- বইয়ের নামঃ মৌলবাদের উৎস সন্ধানে
- লেখকের নামঃ ভবানীপ্রসাদ সাহু
- বিভাগসমূহঃ গল্পের বই
০. মুখবন্ধ / তথ্যসূত্র (মৌলবাদের উৎস সন্ধানে)
ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ধর্মীয় মৌলবাদ,-একই বৃত্তের এ তিনি বিষফুল মানুষের সমস্ত মানবিকতা ও সুস্থ অস্তিত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। এর মধ্যে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় ৫০ বছর আগে ঘটেছিল। কিন্তু সে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় নি, রেখে গেছে তার অন্য দুই সখীকে, তাদের মধ্যে রেখে গেছে তার বিষের নির্যাসটুকুও। সাম্রাজ্যবাদ তার পরিমার্জিত বীভৎসতা নিয়ে এবং দুঃসংবাদ তার নৱাকাসিস্ট চরিত্র নিয়ে এখন মানুষের সমাজ ও সভ্যতার সবচেয়ে বড় দুই শত্রু।
কৈশোরের সেই পুঁজিবাদ আছে কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ নেই, আর অনাবিল ধর্মবিশ্বাস আছে কিন্তু ধর্মীয় মৌলবাদ (ও সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা) নেই।–তাহলে কি সুন্দরই না হত পৃথিবীটা। কিন্তু মানুষ ইতিহাসের পথ বেয়ে ঐ সময় পেরিয়ে এসেছে। পশ্চাদ গমনে ঐ সময়ে তার আর ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। ক্রমশ পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতি ও বিকশিত বৈজ্ঞানিক চেতনায়, বৈষম্যভিত্তিক শোষণজীবী ঐ পুঁজিবাদ ও অলীক ঐশ্বরিক শক্তিকেন্দ্রিক ঐ ধর্ম-উভয়ের অস্তিত্বই ক্রমশ বিপন্ন হয়ে উঠেছে। সৃষ্টি আসন্ন নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও মানবিক অনুশাসনের। কিন্তু তা স্ববিরোধিতায় ভরা, নিজেদের সংকট নিজেরাই সৃষ্টি করছে। তা মানুষের সভ্যতার অগ্রগমনের বিরোধী, তার অস্তিত্বের পরিপন্থী। তাই নতুন মানব সমাজকে তাদের পথ ছেড়ে দিতেই হবে।–হয়তো কয়েক দশক বা দু’এক শতাব্দী পরে। কিন্তু ইতিহাসের আপনি নিয়মে তা হয়ে যাবে, এমন নিয়তিবাদী স্বতস্ফুর্ততানির্ভর চিন্তা বিপজ্জনক। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে তা এমন অপশক্তিগুলির অত্যাচারকে বাড়িয়ে তুলবে ও অস্তিত্বকে প্রলম্বিত করবে। মাত্র। তাই পৃথিবীর শুভবুদ্ধিসম্পন্ন অসংখ্য মানুষ একক ও যৌথভাবে এদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন।
এদের এক ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশীদার হয়ে সামান্য এই বইটির বিনম্র উপস্থাপনা। এটি একটি সাধারণ আলোচনা মাত্ৰ-কোন গবেষণাগ্রন্থ নয়, তথ্যসমৃদ্ধ পণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থও নয়; তার সহজ কারণ ঐ ধরনের সামর্থ্য আমার নেই। তবু যদি এটি বিশেষত ধর্মীয় মৌলবাদ, তথা সামগ্রিক মৌলবাদী মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে পাঠকদের সামান্য কিছুও সাহায্য করে, তবেই তার সার্থকতা।
বইটির পেছনে অনেকের সাহায্যই জড়িয়ে আছে। এদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তবে বিভিন্ন বইপত্র দিয়ে, পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়ে এবং নানা তথ্য সরবরাহ করে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে শ্ৰীমতী মুক্তি চ্যাটাজী, ডঃ অমলেন্দু দে, অশোক রায়চৌধুরী, প্ৰদীপ বসু (রমুদা), সুপ্রিয় দে, ডাঃ আরতি সাহু (চট্টোপাধ্যায়) প্ৰমুখের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতেই হয়। এছাড়া, দিব্যদৃতি পাল, স্নিগ্ধজ্যোতি পাল ও অভ্রজ্যোতি পাল,-উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দিরের এই তিন ভাই আর কম্পোজিটাররা যে উৎসাহ দিয়েছেন ও সহযোগিতা করেছেন, তার জন্য এদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।
ডাঃ ভবানীপ্ৰসাদ সাহু
১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫
দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা
ধর্মীয় মৌলবাদ ও নানা ধরনের মৌলবাদী মানসিকতা এখন বিচ্ছিন্নভাবে হলেও পৃথিবীর নানা এলাকায় তার শক্তি প্ৰদৰ্শন করছে। সম্প্রতি আফগানিস্থানে তালিবানদের উদ্বেগজনক উত্থান এর অন্যতম একটি পরিচয়। সমস্ত মানবপ্রেমিক মুক্তচিন্তার মানুষ এই ধরনের অপশক্তিকে প্রতিহত করার নিরস্তর প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। তবু যেন ইতিহাসের কোন এক অলঙঘ্য নিয়মে,-হয়তো বা মানুষের ক্রমবর্ধমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যখন অলীক ঈশ্বর ও কৃত্রিম ধর্মপরিচয়কে বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বের দ্বারা প্ৰতিস্থাপিত করতে চলেছে, তখন তার প্রতিক্রিয়ায় বিশেষত ধর্মীয় মৌলবাদী, পুনরভু্যুত্থানবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তি তার ক্রমন্ধীয়মান পেশিগুলির আস্ফালন করে। এ অবস্থায় এদের বিরোধীদের আরো সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসার প্রয়োজন। এবং এই প্রয়োজনের প্রসঙ্গেই বাংলা ভাষায় ছোট্ট এই বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ মনে আশা জাগায়। অল্প কিছু সংযোজন ও পরিমার্জন সহ এই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। আশা করি এটিও তার যথাসাধ্য ভূমিকা রাখার প্রচেষ্টায় সফল হবে।
ডাঃ ভবানীপ্ৰসাদ সাহু
১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭
তথ্যসূত্ৰ
১) Dialectical Materialism, Maurice Cornforth, National Book Agency Private Ltd., Calcutta, 1971.
২) The Problem of Hindu Muslim Conflicts; S.R. Bhat, Naba-Karnataka Publications Pvt. Ltd., Karnataka, 1990.
৩। আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতা, বিপানচন্দ্ৰ, (কুণাল চট্টোপাধ্যায় অনুদিত), কে পি বাগচি। অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৮৯
৪। বিশ্ব যখন উথালি পাথাল; ক্রিস্টোফার হিল (অমলেন্দু সেনগুপ্ত ও তরুণ বসু সম্পাদিত), কে পি বাগচি। অ্যাণ্ড কোম্পানি, কলিকাতা ১৯৯৫
৫। খাকি প্যান্ট গেরুয়া ঝাণ্ডা; তপন বসু, প্ৰদীপ দত্ত, সুমিত সরকার, তনিকা সরকার, সম্বুদ্ধ সেন (সুভাষীরঞ্জন চক্রবর্তী অনূদিত), ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা, ১৯৯৩
৬) History of Modern Bengal, Part I; R. C. Majumder, G. Bharadwaj & Co., Calcutta, 1978.
৭। নারী অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে; আউগুস্ট বেবেল, (কনক মুখোপাধ্যায় অনূদিত), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৯৮৩
৮। ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা; গৌতম নিয়োগী, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ১৯৯১
৯। ধর্ম, সংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িকতা; বদরুদ্দীন উমর, চিরায়ত প্রকাশন প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৯৯৩
১০। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন নির্বাচিত রচনাবলি; (প্ৰগতি প্রকাশন অনুদিত), প্ৰগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮১
১১। সাম্প্রদায়িকতা ও ভারত ইতিহাস রচুনা, রমিলা থাপার, হরবংশ মুখিয়া, বিপানচন্দ্ৰ, (তনিকা সরকার অনুদিত) কে পি বাগচি। অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৯৮৯
১২) Ancient India. as describeed by Megasthenes and Apprian, (translated by J. W. McCrindle) (edited by R.C. Majumder), Chucker vertty, Chatterjee & Co. Calcutta, 1960.
১৩। সংস্কৃতির সংকট, বদরুদ্দিন উমর, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৪ ১৪। সংস্কৃতি ও সংস্কৃতিতত্ত্ব; বুলবুল ওসমান, ঢাকা, ১৯৭৭ ১৫। সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতি; নারায়ণ চৌধুরী সম্পাদিত, এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোম্পানি প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৩৮৪
১৬। অতিক্রান্ত, স্মরণে বরণে চতুর্দশ শতক; সম্পাদনা-গোলাম মোর্তোজা, কাজী মোস্তাফিজুর রহমান, মোখলেস হোসেন, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৩
১৭। নতুন দৃষ্টিতে ইতিহাস; আবদুল হালিম, ত্রয়ী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৮। প্রাচীন ভারতে শূদ্র, রামচরণ শর্ম, (শিবেশ কুমার চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র পালিত, স্নেহোৎপল দত্ত অনুদিত এবং রামকৃষ্ণ ভট্টাচাৰ্য সম্পাদিত) কে পি বাগচি। অ্যাণ্ড কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৮৯
১৯। মন ও জড়বাদ; এরভিন শ্রয়েডিংগার (পূর্ণিমা সিংহ অনূদিত), বাউলমন প্রকাশন, ১৯৯০
২০। জাতি-ধর্ম ও সমাজ বিবর্তন; যতীন বাগচী, সঞ্জীব প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯০
২১। বিজ্ঞান ও মার্কসীয় দর্শন; জে বি এস হ্যালডেন, (তারাপদ মুখোপাধ্যায় অনূদিত), চিরায়ত প্রকাশন প্রাঃ লিঃ, ১৯৯০
২২। নৃতত্বের সহজপাঠ; জে, ম্যানচিপ হােয়াইট (মাহমুদা ইসলাম অনুদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২
২৩। প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য; সুকুমারী ভট্টাচার্য, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা, ১৩৯৪
২৪। মার্কসীয় অর্থনীতি, হায়দার আকবর খান রনো, গণসাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৩৯৪
২৫। বিজ্ঞানের ইতিহাস (১ম ও ২য় খণ্ড); সমরেন্দ্ৰ নাথ সেন, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স, কলিকাতা, ১৯৬২
২৬। ভারতীয় জাতি বর্ণপ্ৰথা; নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ফার্মা কে এল এম প্রাঃ লিঃ, কলিকাতা ১৯৮৭
২৭। সংশয়ী রচনা; বাট্ৰান্ড রাসেল (আহমদ ছফা অনুদিত), খান ব্রাদার্স অ্যান্ড কোম্পানি, ঢাকা, ১৯৯৩
২৮) মন্ত্রতন্ত্র কাব্য; আরশাদ আজিজ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫
২৯) Encyclopaedia Britannica, USA Edn., 1987
৩০। বিচ্ছিন্নতার ভবিষ্যৎ, ২য় খণ্ড; ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স পরিবেশিত, কলিকতা, ১৯৮৮
৩১। ধর্মের উৎস সন্ধানে (নিয়ানডার্থাল থেকে নাস্তিক); ভবানীপ্ৰসাদ সান্থ, প্রবাহ,” কলিকতা, ১৯৯২
৩২) …
৩৩) Myth and Reality; Damodar Dharmanand Kosambi; Popular Prakashan, Bombay, 1992
৩৪) The Question of Faith; Rustom Bharucha; Orient Longman, New Delhi, 1993
৩৫। আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস (রূপরেখা); সুশীতল রায়চৌধুরী, নিউ বুক সেন্টার, কলকাতা, ১৯৮৩
৩৬। সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলে বাংলাদেশের অর্থনীতি; অজয় দাসগুপ্ত ও মাহবুর জামান, প্রাচ্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৫
৩৭। গান্ধী রচনা সম্ভার, গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি, পঃ বিঃ, ১৯৭০ ‘ ৩৮। বাংলাদেশের জনবিন্যাস ও সংখ্যালঘু সমস্যা; অমলেন্দু দে, রত্ন প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৭০
৩৯। ভারতের সভ্যতা ও সমাজবিকাশে ধর্মশ্রেণী ও জাতিভেদ; সুকোমল সেন, ন্যাশন্যাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা, ১৯৯৩
৪০। যুদ্ধ যুগে যুগে; গোলাম মোর্তোজা ও কাজী মোস্তাফিজুর রহমান সম্পাদিত, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৯৫
৪১। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা; সুকুমারী ভট্টাচার্য, দীপ প্রকাশন, ১৯৯৭। ইত্যাদি
এবং আনন্দবাজার পত্রিকা, আজকাল, উৎসমানুষ, অনীক, পশ্চিমবঙ্গ, দেশ, প্রতিদিন, The Statesman, Asian Age, The Rationalist News (Australia), International Socialism, Frontier, Monthly Review ইত্যাদির বিভিন্ন সংখ্যা।
১. মৌলবাদ-একটি ‘আধুনিক’ পরিভাষা
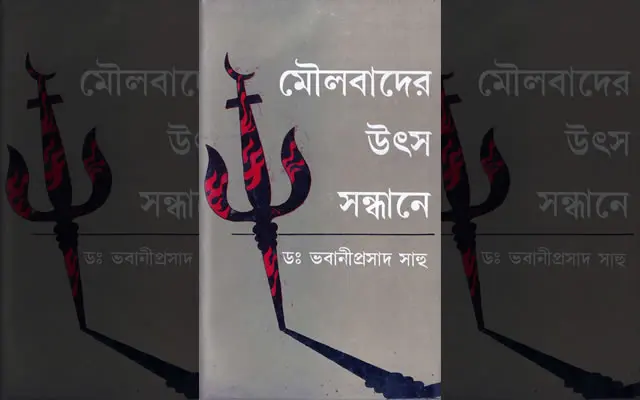
মৌলবাদের উৎস সন্ধানে – ভবানীপ্রসাদ সাহু
মৌলবাদ-একটি ‘আধুনিক’ পরিভাষা
বাংলা ভাষায় ‘মৌলবাদ’ কথাটি খুব বেশি দিন চালু হয় নি। সত্যি কথা বলতে কি চলন্তিকা, এ. টি. দেব, সাহিত্য সংসদের বাংলা-বাংলা বা বাংলা-ইংরেজি অভিধান, কিংবা কাজী আবদুল ওদুদ-আনিলচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত ‘ব্যবহারিক শব্দ কোষ’–এ ধরনের বিভিন্ন অভিধানে ‘মৌলবাদ’ কথাটিই অনুপস্থিত। এসব অভিধানে ‘অধ্যাত্মবাদ’, ‘মতবাদ’ থেকে ‘সাম্যবাদ’, ‘পুঁজিবাদ’—নানা শব্দই রয়েছে, কিন্তু ‘মৌলবাদ’ শব্দটি একেবারেই বাদ। তবে IPP-এর ‘আধুনিক বাংলা অভিধান’- এ ‘মৌলবাদ’ শব্দটি রয়েছে এবং এর অর্থ বলা হয়েছে ‘ধর্মীয় গোঁড়ামির ফলে জাত সংকীর্ণ মতবাদ’। অন্যদিকে সাহিত্য সংসদের ইংরেজি-বাংলা অভিধানে ‘fundamentalism’ কথাটির অর্থ বাংলায় বলতে গিয়েও ‘মৌলবাদ’ উল্লেখ করা হয় নি, বলা হয়েছে। ‘বাইবেল বা অন্য ধর্মশাস্ত্রের বিজ্ঞানবিরুদ্ধ উক্তিতেও অন্ধবিশ্বাস।’ কিন্তু যথাসম্ভব এই fundamentalism কথাটিরই বাংলা অনুবাদ করে ‘মৌলবাদ’ কথাটি চালু করা হয়েছে। তবে তা যে বেশি দিনের ব্যাপার নয়, তা স্পষ্ট। হলে সব বাংলা অভিধানে অন্তত তার উল্লেখ থাকতো। বর্তমানে কথাটি যেভাবে চালু হয়েছে এবং সংবাদপত্র, প্রবন্ধ, রাজনৈতিক শ্লোগান, বিভিন্ন সংগঠনের প্রচারপত্র ইত্যাদিতে যেভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাতে আশা করা যায়, আর কয়েক বছর পরোকার সংস্করণে ঐ সব অভিধানেও কথাটি অন্তর্ভুক্ত হবে।
মূল + ষ্ণ = মৌল ; এই সম্পর্কিত যে মানসিকতা বা মতবাদ আক্ষরিকভাবে তাই-ই মৌলবাদ। মৌল কথাটির অর্থ অনেকভাবেই দেওয়া হয়েছে অভিধানে। তার কয়েকটি হল মূল হইতে আগত, আদিম, প্রাচীন (মৌল আচার) ইত্যাদি। বিমলকৃষ্ণ মতিলাল তার ‘মৌলবাদ—কি ও কেন?’ প্রবন্ধে বলেছেন, ‘ফাণ্ডামেন্টালিজম’ এর বাংলা প্রতিশব্দ তৈরী করা হয়েছে–মৌলবাদ–একেবারে সংস্কৃত ঘেঁষা প্রতিশব্দ– ‘মূল’ থেকে ‘মৌল’। বন্ধু গায়ত্রী চক্রবতী-স্পিভাক বলেন ‘ভৈত্তিকতা’–’ফাণ্ডামেন্টালিজম’-এর প্রতিশব্দ হওয়া উচিত। ‘ভিত্তি’ অথবা ‘ফাউণ্ডেশান’ থেকে। আমি ‘মৌলবাদ’কে গ্ৰহণ করলাম।
‘ভিত্তি’-কে আঁকড়ে রাখার যে প্রবণতা তাকে ‘ভৈত্তিকতা’ বলা যায়; এই ভিত্তি কোন বিশেষ চিন্তাপদ্ধতি, মতাদর্শ, ধর্মমত ইত্যাদির ভিত্তি হিসেবে যে কথাবার্তা বলা হয়েছিল তাকেই বোঝায়। কিন্তু এই অর্থে, মৌলবাদের বিকল্প কথা হিসেবে ‘ভৈত্তিকতা’ শব্দটি আর কেউ ব্যবহার করেছেন বা তার প্রস্তাব দিয়েছেন। কিনা জানা নেই।
অন্যদিকে ‘মৌলবাদ’ শব্দটির ব্যবহার বিগত শতাব্দীতে এমন কি এই বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও আদৌ হয়েছিল বলে মনে হয় না। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্ৰ বা রবীন্দ্রনাথ–বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যাদের হাতে শৈশব পেরিয়ে যৌবনে পদার্পণ করেছিল, তাঁরা ধর্ম, ধর্মীয় গোড়ামি, ধর্মীয় কুসংস্কার, ধর্ম সম্প্রদায় ও সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি প্রসঙ্গে বহু আলোচনা করলেও তাদের লেখায় কোথাও মৌলবাদ শব্দটি সাধারণভাবে চােখে পড়ে না। এটি অবশ্যই ঠিক যে, তাদের প্রতিটি লেখা খুঁটিয়ে পড়ে তারপর এমন মন্তব্য করা হচ্ছে তা নয়। উপযুক্ত গবেষক ও মনোযোগী পাঠক এ ব্যাপারে আলোকপাত করতে পারবেন। তবে এতে অন্তত কোন সন্দেহ নেই যে, বিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশকে (বিশেষত আশির দশকের শেষার্ধ থেকে, রাম জন্মভূমি-বাবরি মসজিদ বিতর্কের প্রসঙ্গে) বাংলা ভাষায় এই শব্দটি পূর্বেকার কয়েক শত বছরের তুলনায় এত বেশি ব্যবহৃত হচ্ছে যে, শব্দটির উদ্ভবই এই সময়ে ঘটেছে বলে বলা যায়।
এই শব্দটির এমন সৃষ্টি ও বহুল ব্যবহারের জন্য ‘ধন্যবাদ’ প্রাপ্য এখনকার হিন্দুত্ববাদী ও ইসলামী জঙ্গী গোষ্ঠীগুলির। এই অর্থে হিন্দু, খৃস্ট বা ইসলামের ইতিহাস ধর্মান্ধ ও গোড়া হিসেবে তার অনুসরণকারী ব্যক্তিদের একটি অংশকে প্রতিষ্ঠা করলেও এবং একটি বিশেষ গোষ্ঠী হিসেবে পাশ্চাত্যে ‘Fundamentalist’— দের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা শতাধিক বৎসর পূর্বে ঘটলেও বাংলা ভাষায় ‘মৌলবাদ’ ‘মৌলবাদী’ কথা দুটি বিশেষ মানসিকতাকে ও ঐ মানসিকতার ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে বােঝাতে এত সুনির্দিষ্টভাবে আশির দশকের আগে ব্যবহৃত হয়নি। এর একটি বড় কারণ আধুনিক ইসলামী মৌলবাদের আবির্ভাব ঘটেছে। ৭০-এর দশকের শেষের দিকে, ইরান ও আফগানিস্থানে। আর শিবসেনা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, ভারতীয় জনতা পার্টি ও তার অন্যান্য সহযোগী সংগঠনগুলি এই আধুনিক বিশ্বে, ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে ঘোষিত ভারতের বুকে বসে ধর্মীয় সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা ও অসহিষ্ণুতার যে চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে ও ঘটাচ্ছে এবং ধর্মান্ধ গোষ্ঠীগুলিও যে একই অ-সভ্য আচরণ করেছে, এসবের প্রভাবে কোন এক সময় কোন লেখক বা সাংবাদিক এমন একটি গ্রহণযোগ্য শব্দ ব্যবহার করে বসেছেন। তাঁর মাথায় যথাসম্ভব ঐ Fundamentalism বা Fundamentalist-দের উদাহরণ ছিল অর্থাৎ একেবারে স্বাধীনভাবে এই শব্দটি যে সৃষ্টি হয়েছে তা নয়। শ্ৰদ্ধেয় পণ্ডিত শ্ৰী বিমলকৃষ্ণ মতিলালও এই অনুমানই করেছেন। অর্থাৎ ঐ সময় এখানে গুণগতভাবে Fundamentalism-এর সঙ্গে তার সাদৃশ্যও খুঁজে পাওয়া গেছিল।
রামমোহন রায় তাঁর ‘সহমরণ বিষয় প্ৰবৰ্ত্তক ও নিবৰ্ত্তকের সম্বাদ’ (১৮১৮-১৯) লেখায় বলেছিলেন, “যে সকল মূঢ়েরা বেদের ফলশ্রবণবাক্যে রত হইয়া আপাত প্রিয়কারী যে ওই ফলশ্রুতি তাহাকেই পরমার্থসাধক করিয়া কহে আর কহে যে ইহার পর অন্য ঈশ্বরতত্ত্ব নাই” ইত্যাদি। এখন এই মানসিকতার কথা বলতে গিয়ে মৌলবাদ বা মৌলবাদী কথাগুলি যুৎসইভাবে কোথাও হয়তো বসিয়ে দেওয়া যেত।
১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ তারিখে স্বামী বিবেকানন্দ শিকাগো ধৰ্মসভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অভ্যর্থনার উত্তরে বলেছিলেন, “সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা ও এসবের ফলস্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল ধরে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। পৃথিবীতে এরা তাণ্ডব চালিয়েছে, বহুবার পৃথিবীকে নরশোণিতে সিক্ত করেছে, সভ্যতাসংস্কৃতি ধ্বংস করেছে এবং সমগ্র মানবজাতিকে নানা সময়ে বিভ্রান্ত, হতাশায় নিমগ্ন করেছে। এই সব ধর্মোন্মাদ পিশাচ যদি না থাকত, তবে মানবসমাজ আজ যে অবস্থায় উপনীত হয়েছে, তার থেকে কত সুন্দর হয়ে উঠতে পারত; এরা তা করতে দেয়নি!” এই ‘ধর্মোন্মাদ পিশাচরা’ ধর্মীয় মৌলবাদীরাই। কিন্তু তখন অন্তত বিবেকানন্দ ‘Fundamentalism’ বা ‘মৌলবাদী’ তথা ‘মৌলবাদী’ কথাগুলি ব্যবহার করেন নি।
এই মৌলবাদ ও মৌলবাদীদের বােঝাতে রবীন্দ্রনাথ ‘ঈশ্বরদ্রোহী পাশবিকতা’, ‘গোঁড়ামি’, ‘ধর্মের বেশে মোহ’, ‘পৌরোহিত্য শক্তি’, ‘সাম্প্রদায়িক ঈর্ষাদ্বেষ’, ‘ধর্মবিকার’, (ধর্মের নামে) ‘মানুষের উপর প্রভুত্ব’ ইত্যাদি নানা শব্দ ব্যবহার করেছেন।
“… তখন ব্রাহ্মণ তো কেবলমাত্ৰ যজন-যাজন অধ্যয়ন লইয়া ছিল না–মানুষের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল। তাই ক্ষত্ৰিয়-প্ৰভু ও ব্রাহ্মণ-প্ৰভুতে সর্বদাই ঠেলা ঠেলি চলিত; বশিষ্ঠে বিশ্বামিত্রে আপস করিয়া থাকা শক্ত।’ (লড়াইয়ের মূল, কালান্তর; পৌষ ১৩২১)
“… মুষলধারে নামিল বেহার অঞ্চলে মুসলমানের প্রতি হিন্দুদের একটা হাঙ্গামা। অন্য দেশেও সাম্প্রদায়িক ঈর্ষাদ্বেষ লইয়া মাঝে মাঝে তুমুল দ্বন্দ্বের কথা শুনি। আমাদের দেশে যে বিরোধ বাধে সে ধর্ম লইয়া, যদিচ আমরা মুখে সর্বদাই বড়াই করিয়া থাকি যে, ধর্মবিষয়ে হিন্দুর উদারতার তুলনা জগতে কোথাও নাই।” (ছোটো ও বড়, কালান্তর; অগ্রহায়ণ, ১৩২৪)
“এ কি হল ধর্মের চেহারা? এই মোহমুগ্ধ ধর্মবিভীষিকার চেয়ে সোজাসুজি নাস্তিকতা অনেক ভালো। ঈশ্বরদ্রোহী পাশবিকতাকে ধর্মের নামাবলী পরালে যে কী বীভৎস হয়ে ওঠে তা চোখ খুলে একটু দেখলেই বেশ বোঝা যায়।” (৮ বৈশাখ, ১৩৩৩-এ শান্তিনিকেতনে দেওয়া ভাষণ)
‘ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মারে।”
কিংবা
“হে ধর্মরাজ ধর্মবিকার নাশি,
ধৰ্মমূঢ়জনেরে বাঁচাও আসি।” (পরিশেষ, রচনাকাল ১৯২৬)
রবীন্দ্রসৃষ্টির বিপুল ব্যাপ্তির মধ্যে মৌলবাদী মানসিকতা ও মৌলবাদী গোষ্ঠীর প্রতি তীব্ৰ কাষাঘাতের চিহ্ন ছড়িয়ে আছে, যদিও তিনি ব্ৰহ্মা বা ঈশ্বর জাতীয় একটি অলীক মায়াময় সত্তায় গভীর বিশ্বাসও পোষণ করতেন। অবশ্যই এ তাঁর নিজস্ব বিশ্বাসের ব্যাপার; কিন্তু শুভবুদ্ধি, মনুষ্যত্ব ও মানবসভ্যতার মঙ্গলকর দিকের প্রতি তাঁর আন্তরিক আস্থা তাঁকে ধর্মের নামে এই ‘মোহমুগ্ধ ধর্মবিভীষিকার’ ও ‘পাশবিকতার’ বিরুদ্ধে সোচ্চার করেছে। তবু তাঁর এই বিশাল সৃষ্টিতে শেষ অদিও ‘মৌলবাদী বা ‘মৌলবাদী’ কথাগুলির আবির্ভাব ঘটে নি।
বিদ্যাসাগর থেকে শরৎচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় থেকে রাজশেখর বসু-বহু মনীষীই বাংলাভাষায় উগ্র ধর্মান্ধত তথা মৌলবাদের বিরুদ্ধে, তাদের সংগ্রামের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। এদের সাহিত্য ও সৃষ্টির মধ্যে ‘মৌলবাদ’ আসে নি। আর এসব কারণে এই কথাটিকেই এখনকার অনেক প্রবন্ধকার একটি ‘আধুনিক পরিভাষা’ হিসেবে গণ্য করতে শুরু করেছেন। যেমন–
“এই ‘এরা’ কারা? এরাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় ‘পৌরোহিত্য শক্তি’, আধুনিক পরিভাষায় ‘মৌলবাদী শক্তি’।”
কিংবা “রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণ্যশক্তি সম্পর্কে আপন মনোভাব একটুও গোপন রাখেননি। যা বলার তা খোলাখুলি বলেছেন। যে ব্রাহ্মণদের কথা তিনি তুলে ধরেছেন, বিবাকেনন্দ, বৈদান্তিক সন্ন্যাসী হয়েও তাদের বললেন ‘কলির রাক্ষস’। বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিক অভিমতটি তুলে ধরি। ১৮৯২-এ বোম্বে থেকে জুনাগড়ের দেওয়ানকে লিখছেন—’দুষ্ট ও চতুর পুরুতরা (আধুনিক পরিভাষায় যারা মৌলবাদী শক্তি) যত সব অর্থহীন আচার ও ভাঁড়ামিগুলিকেই বেদের ও হিন্দুধর্মের সার বলে সাধারণ মানুষদের ঠকায়, শোষণ চালায়। মনে রাখবেন যে, এসব দুষ্টু পুরুতগুলো বা তাদের পিতৃপিতামহগণ গত চারপুরুষ ধরে একখণ্ড বেদও দেখেনি। সাধারণ মানুষরা উপায়ান্তর না দেখে পুরুতদের ধর্মাচরণের নির্দেশকে মেনে নেয়। এর ফলে তারা নিজেদের হীন করে ফেলে। কলির রাক্ষসরূপী ব্ৰাহ্মণদের কাছ থেকে ভগবান তাদের বাঁচান।’ এই মৌলবাদী শক্তিকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে বিদেশ থেকে বিবেকানন্দের আহ্বান এসে পৌঁছয় ভারতীয় যুবকদের কাছে–” ইত্যাদি (পশ্চিমবঙ্গ, রবীন্দ্রসংখ্যা, ১৪০২-এ তাপস বসুর প্রবন্ধ; বন্ধনীর মন্তব্য তাঁরই)
‘মৌলবাদ’ যে অধুনা প্রচলিত একটি শব্দ তা অন্যরাও স্বীকার করেন। ডঃ গৌতম নিয়োগী তার ‘ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা’ গ্রন্থে (১৯৯১) ‘মৌলবাদী’ ‘পুনরুজীবনবাদ’ ও ‘সাম্প্রদায়িকতা’ এই তিনটিকেই ‘অধুনা প্রচলিত শব্দ’ হিসেবে অভিহিত করেছেন। (পৃঃ ১৫)
এখন মৌলবাদ বা মৌলবাদী কথাগুলি ক্রমশঃ তার বিরল চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে। সংবাদপত্রের প্রাসঙ্গিক প্রতিবেদনে তা একটি সাধারণ শব্দ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারত তথা বিশ্বের নানা স্থানে হিন্দু মৌলবাদী-মুসলিম মৌলবাদীদের সাম্প্রতিক পরিবর্ধিত দাপট ও আস্ফালনকে কেন্দ্র করে যে শব্দ ব্যবহার শুরু হয়েছিল, তা গ্রামেগঞ্জের এমন মানসিকতার লোকেদের জন্যও ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন মুর্শিদাবাদের বাগড়ি ও নদীয়ার করিমগঞ্জ এলাকায় বাউল ফকির দরবেশদের উপর ধর্মীয় অত্যাচারের কথা বলতে গিয়ে এখন বলা হয় ‘মনের এই ভাবকে সিনায় রেখে যাঁরা বাউল সাধনায় জীবনযাপন করছেন, তাদের উপর নেমে এসেছে মৌলবাদীদের হুঙ্কার’ (আজকাল, ২৩ মে, ১৯৯৫); অমিতাভ সিরাজের প্রতিবেদন— “গান গেয়ে একঘরে, জল বন্ধ, জরিমানা”)।
ব্যাপারটা শুধু ভারত বলে নয়,–এই ধরনের মানসিকতা যাদের বা যে সংগঠনেরই আছে তাদের ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটি এখন ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন, “ইংল্যাণ্ডের অনেক কলেজেই দানা বঁধছে ধর্মীয় উত্তেজনা : …রমজানকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের জেরে নাইজিরিয়ার এক কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্র মারা যান।… কলেজের ছাত্রদের সূত্রে জানা গিয়েছে সারা বিশ্বে ইসলামের অনন্ত প্রভুত্ব স্থাপনে বিশ্বাসী মৌলবাদী সংগঠন হিজব-উত-হাহরির-এর সমর্থক একদল পাক ছাত্রের সঙ্গে বাকবিতণ্ডার পরই ছাত্রটি আক্রান্ত হন। … উল্লেখ্য, ইংলণ্ডের অধিকাংশ কলেজেই এই মৌলবাদী সংগঠন নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। …’ (আনন্দবাজার পত্রিকা ; ১৩ই মার্চ, ১৯৯৫)
আমেরিকায় ‘ফাণ্ডামেন্টালিজম’ বিগত শতাব্দীতে উদ্ভূত হলেও এবং বাংলায় মৌলবাদ-মৌলবাদী কথাগুলি সম্প্রতি ব্যবহৃত হলেও, অনেকে এধরনের লক্ষণ দেখে ‘মধ্যযুগীয় মৌলবাদ’ কথাও সাধারণভাবে ব্যবহার করেন। তবে যথাসম্ভব ঐ যুগে এভাবে তাদের চিহ্নিত করা হত না। (“গুজরাট-মহারাষ্ট্র অঞ্চলের জনগণ যে মধ্যযুগীয় মৌলবাদ ও ফ্যাসিবাদের কণ্ঠে জয়মাল্য দিয়েছেন, তা সারা দেশের পক্ষে লজ্জাজনক। এর কুফলও সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য৷”—অনীক, ফেব্রুয়ারী-মার্চ, ১৯৯৫)
কথাগুলি ব্যবহৃত হতে হতে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিক ভাষাগত চরিত্র পেয়ে গেছে এবং ‘মৌলবাদী সংগঠন’-এর মত ‘মৌলবাদী শক্তি’-র মত কথাবার্তাও স্বাভাবিকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ এটিকে একটি সামাজিক (অপ-) শক্তির মর্যাদাও দেওয়া হয়েছে। যেমন, “দেবতার বাণী শুনে চাকরি গেছে শৈলমন্দিরের পূজারীর’ (১৪/৬) শীর্ষক প্রতিবেদনটি পড়ে অত্যন্ত হতাশ হলাম। মুখে যত মত তত পথের মহান আদর্শের অনুসরণ করলেও আমাদের অধিকাংশই অত্যন্ত সন্তৰ্পণে হৃদয়ের নিভৃততম কুঠুরিতে পুষে রাখি এক আদিমতম শ্বাপদকে-ধার দিই তার দাঁতে, নখে; প্রচ্ছন্ন উস্কানী দিই মৌলবাদী শক্তিগুলিকে। তা যদি নাইই হবে তাহলে এই একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায়ও বিশ্বজুড়ে দাপাদাপি করবার মত অফুরান মনস্তাত্বিক রসদ মৌলবাদী শক্তিগুলি পায় কোথা থেকে ?…” (আনন্দবাজার পত্রিকায় অংশুমান কর-এর চিঠি; ৩রা জুলাই, ১৯৯৫। সম্পাদকের পক্ষ থেকে এই বিষয়ের চিঠিগুলির সাধারণ শিরোনাম দেওয়া হয়েছে ‘মৌলবাদের থাবা’। )
বিজ্ঞানসম্মত বস্তুবাদী ইতিহাসচর্চ্চার ‘অন্যতম বলিষ্ঠ প্ৰবক্তা’ ডঃ গৌতম নিয়োগীও তীর ইতিহাস ও সাম্প্রদায়িকতা’ (১৯৯১) গ্রন্থে ১৯৯০-এ লেখা ভূমিকায় লিখেছেন, “এই উপমহাদেশের অন্যান্য দেশেও ভারতের মতোই মৌলবাদী শক্তির যেভাবে উত্থান হচ্ছে, তা সবই ঘটছে ভারত-ইতিহাসকে অনেকাংশে সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা ও বিকৃত করার ফলে।” তিনি আবার ‘সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী’ বলে একটি কথা ব্যবহার করেছেন। (“ভারত-ইতিহাসের যে সাম্প্রদায়িক ভাষ্য হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীরা করে থাকেন, নির্মোহ ধৰ্মনিরপেক্ষ ও বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস-বিচারে, সত্য ও তথ্যনিষ্ঠার নিরিখে তা ধোপে টেকে না।” ঐ; পূঃ ৮২) এখানে স্পষ্টতঃ ধর্মীয় সম্প্রদায়গত বিভেদকে যারা অনড় অচল একটি ব্যবস্থা বলে অন্ধভাবে মনে করে তাদেরই ‘সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী’ আখ্যা দেওয়া হয়েছে, যদিও ‘ধর্মীয় সম্প্রদায়িকতা’ কথাটিও প্রচলিত।
এই একই বইতে মানবতাবাদী বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী শ্ৰদ্ধেয় গৌরকিশোর ঘোষ সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় ‘ধর্মীয় মৌলবাদী’ কথা ব্যবহার করেছেন। (“… যারা ধর্মীয় মৌলবাদী তারা মন্দির মসজিদে ঘা পড়তে না পড়তেই যে কোন অছিলায় দেশের সংহতি, সুস্থিতি নষ্ট করে দিতে চাইবেই, দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাতে চাইবেই।”—ঐ; পৃঃ ৯৯) মৌলবাদী বলতে প্রচলিত অর্থে ধর্মীয় মৌলবাদীদেরই বােঝায়, যদিও মৌলবাদ বা মৌলবাদী একটি বিশেষ মানসিকতা ও ঐ অনুযায়ী ক্রিয়াকাণ্ডকে আর যারা তা পোষণ করে ও ঐ অনুযায়ী কাজকারবার করে তাদের বোঝাতে ব্যবহার করা হচ্ছে। এখানেও শ্ৰী ঘোষ মৌলবাদের বা মৌলবাদী মানসিকতার সামগ্রিকতার মধ্যে, যারা মানুষের তৈরি করা কৃত্রিম ও প্রতিষ্ঠানিক ধর্মমতগুলিকে কেন্দ্র করে তাদের মৌলবাদী মানসিকতার প্রকাশ ঘটায় তাদের বুঝিয়েছেন।
কিন্তু সাধারণভাবে মৌলবাদ বলতে ধর্মীয় মৌলবাদ-কেই বোঝানো হয় এবং এইভাবেই তার প্রাথমিক প্রচলন। (“এটা বোঝায় সময় এসেছে যে মৌলবাদী অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গেলে ধর্মীয় বিশ্বাসবোধে আঘাত পড়বেই। ধর্মের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করতে হবে। মৌলবাদ স্বয়ম্ভু নয়। মৌলবাদের উৎস ধর্ম; ধর্মের রীতিনীতি, অনুশাসন, বাণী, নির্দেশ প্রভৃতি ব্যতীত মৌলবাদের কোনো অস্তিত্ব থাকে না; ধর্মের দ্বারাই মৌলবাদ লালিত ও পালিত।”—-সুজিত কুমার দাশ-এর ‘ধর্মবিশ্বাস, রাষ্ট্র এবং নাগরিক অধিকার’, উৎস মানুষ; সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮)
তবে কেউ কেউ আবার বিশেষ ধর্মের পরিচয়ে বিশেষ মৌলবাদী মানসিকতা ও ক্রিয়াকাণ্ডকে চিহ্নিত করছেন, এমন কি সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরুর মৌলবাদ হিসেবেও বিভাজিত করছেন। (“… হিন্দু মৌলবাদের আত্মপ্রকাশ এবং বাবরি মসজিদ ধ্বংসের কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে, দূরদর্শনে রামায়ণ-মহাভারত প্রদর্শনকে কিছু বুদ্ধিজীবী যখন দায়ী করেন, অবাক হতে হয়।” এবং “সংখ্যালঘু মৌলবাদকে হিন্দুয়ানির চাপে সন্ত্রস্ত জনগোষ্ঠীর আত্মরক্ষার মনস্তত্ব হিসেবে ব্যাখ্যা করলে হিন্দু মৌলবাদের প্রসারের সুযোগ করে দেওয়া হবে।”–শৈবাল মিত্রের মনোলগ (?)-সংকলন ‘স্বৰ্গ কি হবে না কেনা,’ ১৯৯৫)
আর মৌলবাদ মৌলবাদী কথাগুলি শুধু ভারতের বাঙালীর মধ্যে বলে নয়, বাংলাভাষাতেই যে স্থান পেয়ে গেছে, তা বোঝা যায় বাংলাদেশের লেখকরাও কথাটির ব্যাপক ব্যবহার করেছেন দেখে, যথাসম্ভব বেশ আগে থেকেই। “সাম্প্রদায়িকতার পরিবর্তে ধর্মীয় রাজনীতির নতুন সংস্করণ মৌলবাদের রাজনৈতিক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হিন্দু অথবা অন্য কোন সম্প্রদায় নয়। এর লক্ষ্যবস্তু হলো, বিপ্লবের শক্তিসমূহ এবং তাদের তাত্ত্বিক শিক্ষক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ।” (বদরুদ্দিন উমরের ‘বাংলাদেশে মৌলবাদ ও শ্রেণীসংগ্রামের নতুন পর্যায়’, জুলাই, ১৯৮৭এ প্রথম প্রকাশিত।)
“ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার আজকের দিনে শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী পুঁজিবাদ তথা সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে মোক্ষম অস্ত্র। তাই স্বৈরাচার ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন কখনও ধর্মের রাজনীতি ও মৌলবাদবিরোধী আন্দোলন থেকে পৃথক হতে পারে না।…” (বাংলাদেশ লেখক শিবির, ঢাকা কর্তৃক জুলাই, ১৯৮৮-এ প্রকাশিত ‘সাংস্কৃতিক আন্দােলন’ পুস্তিকায় মনিরুল ইসলাম-এর ‘রাষ্ট্রীয় ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি’) কিংবা “বাংলাদেশে মৌলবাদীরা ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং ধর্ম নিরপেক্ষতার মধ্যকার বিরোধটিকে জিইয়ে রাখতে যে কোনো প্রসঙ্গকে তুলে নিতে আগ্রহী। তসলিমা নাসরিনের ইসলাম বিরোধিতা, হিন্দু প্রীতি ও ‘লজ্জা’র প্রকাশ ইস্যু হিসেবে মৌলবাদীদের কাছে খুব লোভনীয়। সিলেটের একটি ক্ষুদ্র মৌলবাদী দল তসলিমা নাসরিনের ইসুতে সিলেটে ধর্মঘট ও হরতাল ডাকে।…” (ফারুক ফয়সল-এর প্রবন্ধ ‘তর্কবিতর্ক এবং তসলিমা নাসরিন’; গোলাম মোর্তোজা ও কাজী মোস্তাফিজুর রহমান সম্পাদিত ‘প্রসঙ্গ নারীবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও তসলিমা নাসরিন’, ঢাকা, ১৯৯৪)
স্পষ্টতই আগেরটিকে মৌলবাদ বলতে সামগ্রিকভাবে মৌলবাদ ও মৌলবাদী মানসিকতা-ক্রিয়াকাণ্ডকেই বােঝানাে হয়েছে; পরেরটিতে বাংলাদেশের মৌলবাদী বলতে মুসলিম মৌলবাদীদেরই বােঝানো হয়েছে, যদিও ‘মুসলিম’ বিশেষণটি উহ্য রয়েছে।
(আর ‘মৌলবী’ ও ‘মৌলবাদী’ কথা দুটির মধ্যে বেশ ধ্বনিগত সাদৃশ্য রয়েছে, যদিও তাদের উৎস ও অর্থ আলাদা। ‘মৌলবী’ কথার অর্থ ইসলামী শাস্ত্ৰে পণ্ডিত মুসলিম। কিন্তু তাদের অনেকের আচরণ এমন হয়ে উঠেছে যে, মৌলবী ও মৌলবাদী প্রায় সমার্থক হয়ে যাচ্ছে এবং পাশাপাশি উল্লেখিত হচ্ছে। যেমন, ‘অন্তঃসত্ত্বাকে মাটিতে পুতে পাথর ছুড়ে মারার ফতেয়া’ : জহিরুল হক, ঢাকা, ২৭ জুলাই–মৌলবাদীরা কতটা অমানবিক, নৃশংস হতে পারে তার নতুন নজির ফের মিলল। এক দরিদ্র অন্তঃসত্ত্বা মেয়েকে অর্ধেক মাটিতে পুঁতে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলার ফতোয় দিয়েছে বাংলাদেশের গাজিপুরের ইসলামপুর গ্রামের মৌলবীরা।…” ইত্যাদি। আজকাল, ২৮.৭.৯৫)
তসলিমা নাসরিনও ১৯৯১-এ বাংলাদেশে প্রকাশিত তার ‘নির্বাচিত কলাম’- এ (এর লেখাগুলি আরো আগে বাংলা দেশের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।) অনেকবার কথাটি ব্যবহার করেছেন। –”মৌলবাদীরা বলে নারীর স্থান ঘরে, সে সর্বদা পর্দার ভেতরে থাকবে, তার বাইরে এসে বিজ্ঞাপন করা বারণ। …মৌলবাদীরা নারীকে উপাৰ্জনক্ষম, স্বনির্ভর ও প্রগতিশীল দেখতে চায় না। …তলিয়ে দেখলে পুঁজিবাদী ও মৌলবাদীর অন্তর্নিহিত সাযুজ্য বেশ ধরা পড়ে। পুঁজিবাদীরা নারীকে যে শৃঙ্খল পরায় তা রঙচঙে বাহারি। আর মৌলবাদীদের শৃঙ্খল সুরা কলমা পড়া, ফু দেওয়া, ফ্যাকাসে। …” (এখানে আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত ‘নির্বাচিত কলাম’- এর তৃতীয় মুদ্রণ থেকে সংগৃহীত)
অন্যদিকে এই ‘ধর্মীয় মৌলবাদীদেরই বোঝাতে নানা প্ৰবন্ধকার অন্যান্য নানা পরিভাষাও ব্যবহার করেছেন। যেমন হিন্দু ধৰ্মীয় মৌলবাদীদের জন্য ‘হিন্দু জাতীয়তাবাদী’ কথাটি। “হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের মনে রাখা উচিত, মহাত্মা গান্ধী অথবা পণ্ডিত নেহরু এমন কোন ‘রথ’ কখনো চালাননি যাতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। আদবানির রথ যাত্রা সম্বন্ধে কি এই কথা বলা যায়?”–ডঃ অমলেন্দু দে-র ‘ধর্মান্ধতাকে চালানো হচ্ছে জাতীয়তার নামে’, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২.১২.৯০। এই ‘ধর্মান্ধতা’ কথাটিও বহু জন ধর্মীয় মৌলবাদের সমর্থক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। (সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে যে সব দম্পতি লড়াই করে আসছেন, তাঁদের মধ্যে একটি প্রখ্যাত নাম, ঐতিহাসিক ও সুলেখক ডঃ অমলেন্দু দে এবং তাঁর স্ত্রী নাসিমা। ডঃ দে তাঁদের বাংলা লেখায় ১৯৯০-এর অগাষ্ট থেকে ‘মৌলবাদ-মৌলবাদী’ কথাগুলি ব্যবহার করছেন বলে জানিয়েছেন। তার আগে, ১৯৭৩ থেকে লিখতেন ‘ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ’, ‘সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যবোধ’ ‘ইসলামিকরণ’ ইত্যাদি কথা। আর বক্তৃতাদিতে ১৯৮০ সাল থেকেই মৌলবাদ-মৌলবাদী ইত্যাদি ব্যবহার করতেন। যাঁরা এ প্রসঙ্গে কাজ করছেন, তাদের অন্যতম একজনের শব্দ ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত রাখার জন্য এখানে এই ব্যক্তিগত উল্লেখ।)
‘হিন্দুত্ববাদী’ কথাটিও হিন্দুমৌলবাদীদের বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। (“…তাঁরা মার্ক্সবাদীই হন আর হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় জনতা পার্টিই হন, তফাৎ ধরা পড়ে কেবল বুকনিতে।।”—আবদুর রউফ-এর ‘মহারাষ্ট্রে নতুন জমানা সাম্প্রদায়িক এবং প্রাদেশিক’, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২১শে মার্চ, ১৯৯৫)
কেউ কেউ আবার ‘হিন্দু দক্ষিণপন্থা’ কথাটি ব্যবহার করেন ‘হিন্দুমৌলাবাদের’ প্রায় সমার্থক হিসেবে। (সুভাষীরঞ্জন চক্রবর্তী অনুদিত তপন বসু প্ৰমুখের ‘খ্যাকিপ্যান্ট গেরুয়া ঝাণ্ড’, ১৯৯৩) তবে এই হিন্দু দক্ষিণপন্থা বা ধর্মীয় দক্ষিণপন্থা (Religious right) শুনলে কেমন একটা খটকা লাগে। তাহলে ‘হিন্দু বামপন্থা’ বা ‘ধর্মীয় বামপন্থা’ নামে কোন কাঁঠালের আমসত্ত্ব হয় নাকি ?
পাশাপাশি বাংলা ‘সাম্প্রদায়িকতা’ শব্দটির কিছু ভিন্নতর ব্যঞ্জনা থাকলেও অনেকে বিশেষত ‘ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা’-কে ধর্মীয় মৌলবাদের কাছাকাছি একটি অর্থে প্রায়শঃই ব্যবহার করেন—এমনকি তার অর্থ আরো প্রসারিতও করেন। (“ভারতীয় রাজনীতিতে ‘সাম্প্রদায়িকতা’ এই শব্দটি আদিতে প্রধানত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের রাজনীতি, বিশেষত হিন্দু-মুসলমান রাজনীতি বোঝাতো। বর্তমানে শব্দটির অর্থ আঞ্চলিকতাবাদ, জন্মলব্ধ বৰ্ণাশ্রমবাদ ও গোষ্ঠীবাদে সম্প্রসারিত হয়েছে।”–ডাঃ ধীরেন্দ্ৰ নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ সাম্প্রদায়িকতা : মনস্তাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ’, মানবমন।)
কেউ আবার ‘সাম্প্রদায়িকতা’ কথাটিকে শুধু ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করেন, মনে হয়, ধর্মীয় মৌলবাদের প্রায় সমার্থক হিসেবে। (“কোনো ব্যক্তির মনোভাবকে তখনই সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া হয় যখন সে এক বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্তির ভিত্তিতে অন্য এক ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচারণ এবং ক্ষতিসাধন করতে প্ৰস্তুত থাকে। এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিবিশেষের ক্ষতিসাধন করার মানসিক প্রস্তুতি সেই ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় অথবা বিরুদ্ধতা থেকে সৃষ্ট নয়। ব্যক্তি বিশেষ এক্ষেত্রে গৌণ, মুখ্য হল সম্প্রদায়।”—বদরুদ্দিন উমর-এর সাম্প্রদায়িকতা’, নবপত্র প্রকাশন)
তবে এঁরা সবাই সচেতন যে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় মৌলবাদ–এ দুটির মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত কিছু পার্থক্য আছে। তাই সাধারণতঃ দুটিকে ভিন্ন ভাবেই ব্যবহার করা হয়। যেমন, ‘ভারতে সাম্প্রদায়িকতার বিপদ যে ক্রমবর্ধমান, এ বিষয়ে বোধহয় বিতর্কের অবকাশ নেই। …সাম্প্রদায়িকতাকে ইন্ধন জোগায় যে ধর্মীয় মৌলবাদ, তার প্রভাবও ক্রমবর্ধমান।” (‘সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় মৌলবাদ’ শিরোনামের মুখবন্ধ; অনীক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৯০)
অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ যেভাবে ‘সাম্প্রদায়িক’, ‘সাম্প্রদায়িকতা’ বা ‘ধৰ্মসম্প্রদায়’ কথাগুলি ব্যবহার করেছেন তা তখন অপ্রচলিত কিন্তু আধুনিক পরিভাষার ‘মৌলবাদী’ ও ‘মৌলবাদের’ কাছাকাছি। (“… সম্প্রদায়ের নামে ব্যক্তিগত বা বিশেষ জনগত স্বভাবের বিকৃতি মানুষের পাপবুদ্ধিকে যত প্রশ্রয় দেয় এমন বৈজ্ঞানিক ভ্রান্তিতে কিংবা বৈষয়িক বিরোধেও না। সাম্প্রদায়িক দেবতা তখন বিদ্বেষবুদ্ধির, অহংকারের, অবজ্ঞাপরতার, মুঢ়তার দৃঢ় আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায়; শ্ৰেয়ের নামাঙ্কিত পতাকা নিয়ে অশ্রেয় জগদব্যাপী অশান্তির প্রবর্তন করে-স্বয়ং দেবত্ব অবমানিত হয়ে মানুষকে অবমানিত ও পরস্পর-ব্যবহারে আতঙ্কিত করে রাখে। আমাদের দেশে এই দুর্যোগ আমাদের শক্তি ও সৌভাগ্যের মূলে আঘাত করছে।” কিংবা “ধৰ্মসম্প্রদায়েও যেমন সমাজেও তেমনি, কোনো এক পূর্বতনকালে যে সমস্ত মত ও প্রথা প্রচলিত ছিল সেগুলি পরবর্তীকালেও আপন অধিকার ছাড়তে চায় না।”—মানুষের ধর্ম, ১৯৩৩)
অন্যদিকে ‘মৌলজীবী’ বলে একটি অদ্ভুত শব্দও ব্যবহার করেছেন কেউ কেউ। প্রচলিত ‘মৌলবাদী’ শব্দটির অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করলেও বুৎপত্তিগত অর্থে শব্দটি একটু খটােমটােই লাগে। (“…কী হিন্দু কী মুসলিম সমস্ত রকমের মৌলজীবীরা নানান ফাঁক ফোঁকর দিয়ে এই অসুস্থ কার্যপ্রবাহটা দাপটের সঙ্গে কায়েম করে চলেছে।” ইত্যাদি। সুজিত সেন-এর ‘সাম্প্রদায়িকতা : রাবীন্দ্ৰিক অভিজ্ঞান’; ‘সাম্প্রদায়িকতা : সমস্যা ও উত্তরণী’, ১৯৯১)
কিন্তু এরই পাশাপাশি এটিও সত্য যে মৌলবাদ-মৌলবাদী কথাগুলিও কিছু ব্যতিক্রমী পদ্ধতিতেই সৃষ্টি হয়েছে। অধ্যাত্মবাদ, পুঁজিবাদ, বিবর্তনবাদ, নারীবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, সমাজবাদ, সাম্যবাদ, গান্ধীবাদ, মতবাদ, মার্কসবাদ ইত্যাদি শব্দগুচ্ছে সব সময়েই একটি বিশেষ্য শব্দের পরে ‘বাদ’ প্ৰত্যয় যোগ করে নতুনতর তাৎপর্যের নতুন শব্দ গঠন করা হয়েছে। কিন্তু মৌলবাদে ‘মৌল’ একটি বিশেষণ। সেক্ষেত্রে ‘মূল্যবাদ’ ও ‘মূল্যবাদী’ কথাগুলি হয়তো প্রচলিত পদ্ধতিগত বিচারে সঠিক হত। তবু কোনভাবে একসময় মৌলবাদ-মৌলবাদী কথাগুলি এত ভালভাবে চালু হয়েছে যে, একে এখন পাল্টানোর প্রচেষ্টা না চালানোই ভাল। সব সময় আগেকার নিখুঁত হিসেব আর নিয়ম মেনে ভাষার বিকাশ ও নতুন শব্দের সৃষ্টি হতেই হবে এমন ‘মৌলবাদী’ ভাবনা না থাকাই মঙ্গল।
তৈরী যেভাবেই হােক না কেন মৌলবাদ-মৌলবাদী কথাগুলি এখন হরদম ব্যবহৃত হচ্ছে। নানা জনে নানা ভাবে তার প্রয়োগ করছেন, অনেক ক্ষেত্রেই একটি অস্পষ্ট বা সাধারণ ভাসা ভাসা অর্থে। তবে সবক্ষেত্রে উগ্ৰ গোড়া ধর্মান্ধ মানসিকতার সঙ্গে তাকে অবশ্যই যুক্ত করা হচ্ছে। কিন্তু আমেরিকার ফাণ্ডামেন্টালিজম-এর অন্যান্য দিকগুলি, –যেমন বিবর্তনবাদ ও কমুনিজম বিরোধিতা কিংবা হান্ধা আমোদপ্রমোদ পরিহার করা ও ধূমপান-মদ্যপান না করার মত আচার-আচরণ, তথা ভোগবাদ বিরোধিতা ইত্যাদিকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ফাণ্ডামেন্টালিজম-এর ভাবগত দিকটিই গ্রহণ করা হয়েছে। তবু আমেরিকায় সৃষ্টি হওয়া ফাণ্ডামেন্টালিজম ও ফাণ্ডামেন্টালিস্টদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে রাখার চেষ্টা করা যায়।
২. ফান্ডামেন্টালিজম ও ফান্ডামেন্টালিস্টরা
বাংলা ‘মৌলবাদ’ কথাটি যে ইংরেজী ‘Fundamentalism’ (ফান্ডামেন্টালিজম)–এর অনুপ্রেরণায় সৃষ্টি (coin) করা হয়েছে তাতে প্রায় কোন সন্দেহ নেই। মৌলবাদ বা Fundamentalism বিগত শতাব্দীতে আমেরিকার প্রোটেস্টান্ট খৃস্টানগোষ্ঠীর মধ্যে উদ্ভূত হয়েছিল এবং খৃস্ট ধর্মের একটি অন্যতম ক্ষুদ্র উপ-গোষ্ঠী হিসেবে স্বাতন্ত্র লাভ করেছে। তবে মানসিকতাটি অতি ব্যাপক। মৌলবাদী বলতে সাধারণভাবে যা বোঝানো যায়। তার চরিত্র ও লক্ষণগুলি এই বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যেও ছিল বা আছে। কিন্তু শুধু মৌলবাদী বা খৃস্টীয় মৌলবাদী বলে Fundamentalist (ফান্ডামেন্টালিস্ট)-দের বোঝানো মুস্কিল, ‘ধৰ্মীয় মৌলবাদী’ বলে তো নয়ই। এই বিশেষ গোষ্ঠীকে বোঝাতে Fundamentalist কথাটিই ব্যবহার করা দরকার। এখনো খৃস্টানদের মধ্যে এঁদের অস্তিত্ব রয়েছে।
এরা একেবারে সাধু-সন্ন্যাসী গোছের না হলেও, এঁদের কিছু নিজস্ব আচার আচরণ বিধিনিষেধ রয়েছে। অধিকাংশ Fundamentalist (ফান্ডামেন্টালিস্ট) ধূমপান করেন না, মদ্যজাতীয় কোন পানীয় গ্রহণ করেন না, নাচে অংশ গ্ৰহণ করেন। না বা নাচেন না এবং এমনকি সিনেমা, নাটক ইত্যাদি দেখেন না। এঁদের নিজস্ব, ফান্ডামেন্টালিস্ট কলেজ ও বাইবেল ইনস্টিটিউট রয়েছে। অন্তত এগুলিতে পূর্বোক্ত বিধিনিষেধগুলি কঠোরভাবে পালন করা হয়। এদের ঈশ্বর উপাসনার পদ্ধতিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু তফাৎ থাকতে পারে, তবে সাধারণতঃ গীর্জ বা যাজকের ভূমিকা তাতে থাকে না। কিন্তু বাইবেলকে অপরিবর্তনীয় বিতর্কাতীত সর্বোচ্চ নেতৃত্বের গ্রন্থ হিসেবে গ্ৰহণ করা এবং প্রাচীন আচারপদ্ধতিকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করার ব্যাপারটি তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আর একসঙ্গে জড়ো হয়ে গান ও প্রার্থনার সঙ্গে ধর্মোপদেশ দেওয়াটা ফান্ডামেন্টালিস্ট উপাসনা প্রক্রিয়ার একটি সাধারণ দিক।
এধরনের বাহ্যিক কিছু দিকের মধ্যে ফান্ডামেন্টালিস্ট-দের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বাইবেলের কোন ধরনের সমালোচনাকে বা পরিবর্তনকে সহ্য না করার মানসিকতা। এর সঙ্গে আধুনিকতা (modernism), আধুনিক মতাদর্শগত বিতর্ক, যুক্তিবাদ ইত্যাদি এবং বিশেষত বিবর্তনবাদ ও এই ধরনের আধুনিক দৈত্য’ (demon)–দের ঘূণার সঙ্গে পরিহার করার মানসিকতাও এঁদের বিশেষ চারিত্রিক লক্ষণ। কিন্তু আধুনিকতার সঙ্গে তাদের এই বিরোধ (Fundamentalist-modernist controversy) আসলে বেশ পরেকার ব্যাপার-প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক নাগাদ এটি পরিষ্কার রূপ পায়।
কিন্তু ফান্ডামেন্টালিজম-এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অনেক আগে এবং এক্ষেত্রেও পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতি, বৈজ্ঞানিক চেতনার ক্রমবিকাশ, অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ৰমপরিবর্তন ইত্যাদির ফলে যখন ধর্মের অস্তিত্ব ও চিরাচরিত। ঐতিহ্যের উপর আঘাত আসতে থাকে তখন তার প্রতিক্রিয়ায় এধরনের চরম প্রতিক্রিয়াশীল মতাদর্শের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সব সময়ে সমাজে নতুন প্রগতিশীল চিন্তাভাবনা যখন আসে, তখন তার বিরুদ্ধে পুরনো চিন্তাভাবনা কিছুকাল। লড়াই চালাতেই থাকে। ধর্মের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি মৌলবাদের রূপ ধারণ করতে পারে এবং জেতার জন্য তার এই লড়াই জঙ্গী, মরিয়া ও আগ্রাসী হয়ে ওঠে। সমাজের কিছু মুক্ত চিন্তার মানুষ জ্ঞান ও সমাজের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পুরনো ধ্যানধারণার পরিমার্জনা-এমনকি বৈপ্লবিক রূপান্তরও ঘটান, কিন্তু অন্য কিছু মানুষ প্রাচীনকেই পরম সত্য বলে আঁকড়ে রাখেন-যা মৌলবাদেরই একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। নতুন চিন্তা যদি সত্য ও শক্তিশালী হয় তবে তার জয় এর ফলে বিলম্বিত হলেও, অবশ্যম্ভাবী। এবং পরবর্তী কালের নতুনতর আরো বিকশিত চিন্তার সঙ্গে তারও দ্বন্দ্ব শুরু হয়, তখন আগেকার একদা প্রগতিশীল চিন্তা প্রতিক্রিয়াশীলের ভূমিকা পালন করে বা করতে পারে। সমাজ বিকাশে এবং এই বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উৎপাদন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক, চিন্তাভাবনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে এধরনের সর্বদা পরিবর্তনশীল দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া অবিচ্ছেদ্য একটি দিক এক সময় যে প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম সমাজে প্রগতিশীল ও প্রয়োজনীয় হিসাবে সৃষ্টি হয়েছিল, কিছু পরে তাইই প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে।
খৃস্টধর্মের জড়বদ্ধতা, বিশেষত তার আচার সর্বস্বতা, কায়েমী স্বার্থের সংকীর্ণতা–এসবের প্রতিবাদে একদা প্রোটেস্টান্ট উপ-বিভাগের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীর্ণ কালে ঊনবিংশ শতাব্দী সময়কালে যে আমেরিকায় ইয়োরোপের শিল্পবিপ্লবের উত্তরসূরী হিসেবে দ্রুত উৎপাদন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পাল্টাচ্ছিল এবং নানা ধরনের উদার চিন্তার উদ্ভব ঘটেছিল, তখন ঐ আমেরিকাতেই ‘আমেরিকান প্রোটেস্টন্টিজম’-এর মধ্যে রক্ষণশীল ধর্মীয় আন্দোলনের ভেতর দিয়ে ‘ফান্ডামেন্টালিজম’-এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল—(১) খৃস্টান ধৰ্মপুস্তকগুলির অপরিবর্তনীয়। আক্ষরিক ব্যাখ্যাকে ও সেগুলির চরম অবস্থানকে খৃস্টধর্মের মৌল (fundamental) ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা, (এখন হিন্দু বা মুসলিম মৌলবাদীরা বেদ-উপনিষদমনুসংহিতা-কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্ৰ-কোরাণ-হাদিস সম্পর্কে যে মনোভাব পোষণ করেন), (২) যিশু খৃষ্ট শিগ্নিরই সশরীরে দ্বিতীয়বার আবির্ভূত হতে যাচ্ছেন-এ সম্পর্কিত বিশ্বাস, (রামরাজ্য বা ইসলামী রাষ্ট্র?), (৩) কুমারী মায়ের গর্ভে তার জন্ম সম্পর্কিত বিশ্বাস (The Virgin Birth), (8) পুনরভ্যুত্থান (resurrection) সম্পর্কিত বিশ্বাস ও (৫) প্রায়শ্চিত্ত (Atonement)।
পরবর্তীকালে, বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে, ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক মানসের বিপরীতে আমেরিকায় ফান্ডামেন্টালিজম পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই শতাব্দীর শেষের দিকে আমেরিকায় তার প্রতিনিধি হিসেবে অসংখ্য ধর্মীয় সংগঠন (Church bodies), শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নানা সংগঠন ও সংস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এখনো এগুলি যথেষ্ট সক্রিয়। (একইভাবে ভারত-বাংলাদেশ-পাকিস্তান সহ নানা দেশে হিন্দু বা মুসলিম মৌলবাদীরাও নানা ধর্মীয় সংগঠন, শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান এবং গণসংগঠন বা রাজনৈতিক সংগঠন, দল, প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে।)
কিন্তু পরের দিকে যাই-ই হোক না কেন, একটু পেছন দিকের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে যিশু খৃস্টের দ্বিতীয় আবির্ভাব (Second Advent of Christ) হতে চলেছে এবং সামনের এক হাজার বছর ধরে অপার শাস্তির যুগ আসছে।–এমন একটি বিশ্বাস ১৮৩০-৪০ সাল নাগাদ আমেরিকায় প্রচণ্ড আলোড়ন ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে। এই ‘একহাজার বছরের আসন্ন শান্তির যুগকে বলা হয় ‘the millennium, (মিল্লেন্নিয়াম) (তুলনীয়, ভারতের হাস্যকর রামরাজ্যের কথাবার্তা) এবং এ সম্পর্কিত ধর্মীয় আন্দোলনের নামই হয় ‘millenarian movement’। এই আন্দোলনের মধ্যেই পরবর্তীকালে সৃষ্টি হওয়া ফান্ডামেন্টালিজম’-এর শেকড় লুকিয়ে আছে। ঐ ধরনের বিশ্বাস, তার প্রচার, তাকে কেন্দ্র করে নানা স্বার্থের নানা ধরনের সাংগঠনিক ধর্মীয় প্রয়াস—এগুলি ‘নায়াগ্রা বাইবেল সম্মেলন’ (Niagara Bible Conference)-এর মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট আন্দোলনে সুসংহত হয়। নিউ ইয়র্ক শহরের ব্যাপটিস্ট যাজক জেমস ইংলিশ (James Inglis)। ১৮৭২ সালে তাঁর মৃত্যুর অল্পদিন আগে এই সম্মেলনের প্রারম্ভিক উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর পর ‘সেন্ট লুই প্রেসবিটেরিয়ান’ (Presbyterian) যাজক জেমস এইচ ব্রুকস (James H. Brooks) (১৮৩০-৯৭)-এর অধীনে এর কাজ চলতে থাকে। জেমস ব্রুকস ছিলেন প্রভাবশালী মিলেনারিয়ান পত্রিকা ‘দি টুথ’-এর সম্পাদক।
তবে এই ‘মিলেনারিয়ান’ আন্দোলনের আগে প্রটেস্টান্ট চার্চের মধ্যে পুনরভ্যুত্থানবাদ বা revivalism নামে আরেকটি ধারার সৃষ্টি হয়েছিল, যা আমেরিকায় এই ফান্ডামেন্টালিজম’-এর সৃষ্টিকে প্রভাবিত করেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইংল্যাণ্ডে এর উদ্ভব হয় এবং পরে উত্তর আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। এই তত্ত্বের নাম থেকেও খৃস্টধর্মের শক্তিকে আবার বাড়িয়ে তোলার আকাঙ্খার ব্যাপারটি বোঝা যায়। এর অনুগামীরা খৃস্টধর্মের প্রভাবকে সংহত করা এবং আরো বিস্তার করার প্রচেষ্টা চালায়। আমেরিকায় প্রসারিত এই ধারাই কয়েক দশক পরোকার মিলেনারিয়ান বিশ্বাস ও পরোকার ফান্ডামেন্টালিজম-এর পথ প্রশস্ত করে।
এই রিভাইভ্যালিজম’-এর উদ্ভবও ধর্ম ও বাইবেল বিরোধী বাতাবরণের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টি। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ইয়োরোপে মূলত দরিদ্র ও সমাজের পিছিয়ে থাকা মানুষদের উদ্যোগে প্রথাবিরোধী বিশ্বাস ও কাজকর্মের একটি তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। ডিগার, র্যান্টার, লেভেলার, কোয়েকার ইত্যাদি নামের নানা গোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে প্রচলিত খৃস্টধর্ম তথা বাইবেলের বিরুদ্ধেবিদ্রোহী চেতনার এবং রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নানা ঐতিহ্যগত প্রাচীন ধারণা ও বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার প্রয়াস সংগঠিত হয়েছিল। র্যান্টাররা বাইবেলকে মনে করতেন যত দুঃখকষ্ট, বিভেদ ও বিশ্বব্যাপী রক্তপাত –এর কারণ। কারো মতে ওটা ধাপ্লাবাজিতে ভরা। কেউ (ওয়ার্ল্ডউইন) বলেছেন, ‘বাইবেল স্ববিরোধিতায় ভর্তি এবং তাকে ঐশী বাণী বলেও গ্রহণ করতে তারা রাজী নন। কেউ (বোথােমলি) বাইবেলকে রূপক হিসেবে গণ্য করেন এবং তাকে কোন সৎ লোকের লেখা যে কোন গ্রন্থের সমতুল্য’ বলে মনে করেন এবং এই ধরনের দু একটি উদাহরণ সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের পরিচায়ক অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র। আপাতত এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে বলা যায় যে, সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও চেতনার বিকাশের অনেক আগেই, ইয়োরোপের শিল্পবিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত কল্পতে ও তার প্রাসঙ্গিকতায় এ ধরনের প্রথাবিরোধী, ধর্মবিরোধী ও বাইবেলবিরোধী তীব্র মতাদর্শ জনগণের মধ্যে গড়ে উঠছিল। একে রুখতে একে একে সৃষ্টি হয়েছিল রিভাইভ্যালিজম, মিলেনারিয়ান আন্দোলন, ফান্ডামেন্টালিজম তথা মৌলবাদ। বিংশশতাব্দীর শেষ প্রান্তে ধর্ম যতই কোণঠাসা হচ্ছে ততই এই হতাশ মৌলবাদও আপ্ৰাণ শেষ লড়াই চালাচ্ছে। সে অন্য প্রসঙ্গ। আপাতত আমরা মিলেনারিয়ান আন্দোলনেই ফিরে যাই।
গোঁড়ার দিকে অন্যান্য মিলেনারিয়ান নেতৃত্বের মধ্যে আরো কয়েকজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন–ব্যাপটিস্ট ইভাঞ্জেলিস্ট জর্জ সি. নীডহ্যাঁম (George C. Needham; ১৮৪০-১৯০২), প্রেসবিটেরিয়ান যাজক উইলিয়াম জে. আর্ডম্যান (William J Erdman; ১৮৩৪-১৯২৩) (বাইবেলের ব্যাখ্যাতা হিসেবে এর বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল), উইলিয়াম আর নিকলসন (William R. Nicholson; ১৮২২-১৯০১),–ইনি ১৮৭৩-এ এপিস্কোপাল চার্চ ছেড়ে ছোট্ট গোষ্ঠী রিফর্মড এপিস্কোপালএর বিশপ হয়েছিলেন।
ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বেষ্টনের বিখ্যাত ব্যাপটিস্ট যাজক অ্যাডোনিরাম (šī ti (Adoniram J. Gordon; ১৮৩৬-১৮৯৫) ও চার্চ অব কানাডায় হুরোনের বিশপ মরিস বন্ডউইন (Maurice Baldwin; ১৮৩৬-১৯০৪)-এর মত ব্যক্তিরাও এই মিলেনারিয়ান আন্দোলনে আকৃষ্ট হন।
১৮৯৯ অব্দি সাধারণত নায়াগ্রা অন দি লোক (ওন্টারিও)-তে এই গোষ্ঠী প্রতি বছর গ্ৰীষ্মে সম্মেলনের আয়োজন করতেন। আর ১৮৭৮ থেকে ঐ নায়াগ্রা সম্মেলনের সঙ্গে যুক্ত মিলেনারিয়ানরা বড় বড় শহরেও বহু প্ৰকাশ্য সম্মেলনের পৃষ্ঠপোষকতা করতে শুরু করেছিলেন যেমন নিউইয়র্ক শহরের ‘বাইবেল অ্যাণ্ড প্রফেটিক কনফারেন্স’।
আমেরিকায় এ ধরনের মিলেনারিয়ান আন্দোলনের সূত্রপাতের সঙ্গে স্পষ্টভাবে সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন, সংকট, ঘাত-প্ৰতিঘাত ও ঘটনাবলীর সম্পর্ক ছিল। আমেরিকায় ক্রমশঃ মাথা চাড়া দেওয়া শ্রমিক বিক্ষোভ, সামাজিক অসন্তোষ ও ক্রমবর্ধমান রোমান ক্যাথলিক অনুপ্রবেশের কারণে কিছু প্রোটেস্টান্ট নেতৃত্বের মধ্যে আমেরিকার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়। (তুলনীয়, ভারতে মুসলিম অনুপ্রবেশ’-এর কারণে ভারতের অর্থনীতি, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদি বিপন্ন হচ্ছে বলে হিন্দু মৌলবাদীদের আশঙ্কা ও দেশের রুগ্ন অর্থনীতি ও কায়েমীস্বার্থের সামাজিক অবস্থানের অনিশ্চয়তা এই আশঙ্কা যথার্থ বলে বিশ্বাস করতে তাদের সাহায্য করে—যদিও এই রুগ্নতার কারণ তা নয়।) এছাড়া নতুনতর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকের শেষের দিকে ও নবম দশকে আমেরিকায় বাইবেলের মত তথাকথিত পবিত্র ধর্মগ্রন্থের সমালোচনামূলক মুক্তচিন্তার প্রচার ও প্রসারও তখন ঘটছিল; এর প্রতিক্রিয়াতেও ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের একাংশ এই গোঁড়া, ধর্মীয় ঐতিহ্য অনুসারী মিলেনারিয়ান আন্দোলনে আকৃষ্ট হন। এবং তাকে ধৰ্মরক্ষার (তথা দেশকে রক্ষার) একটি উপায় বলে বিশ্বাস করেন। (ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইয়ংবেঙ্গল বা রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সমাজ-সংস্কারমূলক আন্দোলনের স্তর পেরিয়ে এবং তার প্রতিক্রিয়ায় এই বাংলাতেও গোঁড়া হিন্দুত্ববাদের আবির্ভাব ঘটে—বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শশধর তর্কচূড়ামণি জাতীয় বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বে।)
ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে প্রোটেস্টান্ট ইভানজেলিস্ট ডুইট এল মুডি (Dwight L. Moody; ১৮৩৭-৯৯)। নর্থফিল্ডে তার সমাবেশগুলিতে মিলেনারিয়ান চিস্তাভাবনার প্রকাশের ক্ষেত্রে একটি প্রভাবশালী কর্মপন্থা উপস্থাপিত করেন। বিদেশে গিয়ে ধর্মপ্রচার তথা মিশনারী কাজকর্ম করাকে মিলেনারিয়ানরা সমর্থন ও উৎসাহিত করেন!! (হিন্দু বা মুসলিম মৌলবাদীরাও বিদেশের নানা স্থানে নিজেদের শাখা প্রতিষ্ঠা করছেন।) এর ফলশ্রুতিতে এ ধরনের মিশনারী উৎসাহ ও কাজকর্ম উত্তাল তরঙ্গের আকারে বিস্তার লাভ করে এবং একসময় তা ‘স্বেচ্ছাসেবী ছাত্র আন্দোলন’ (Student Volunteer Movement বা SVM) নামে বিশ্বষ সাংগঠনিক রূপ পায়। তাঁরা নিউ জার্সির প্রিন্সটনে প্রিন্সটন থিওলজিক্যাল সোসাইটি’ (প্রিন্সটনের ঈশ্বরতাত্ত্বিক সংস্থা)-র মধ্যে কিছু অধ্যাপক তথা বিদ্বান ব্যক্তিরও সন্ধান পান যাঁরা বাইবেলের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব ও প্রেরণাকে কঠোরভাবে রক্ষা করতে আগ্রহী। প্রিন্সটনের এই অধ্যাপকদের মিলেনারিয়ানরা নিজেদের সভা-সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানান এবং বাইবেলের সমর্থনে তাদের বক্তব্যগুলিকে নিজেদের মত করে গ্রহণ করেন। বাস্তবত প্রিন্সটনের এই সব ব্যক্তিদের প্রায় কেউই মিলেরিয়ানদের মতবাদকে গ্ৰহণ করেন নি, কিন্তু উভয়পক্ষই বাইবেলের কর্তৃত্বের প্রশ্নে উভয়ের সমর্থনকে সম্মান জানান ও স্বীকার করেন।
(প্ৰসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, আমেরিকায় ধর্ম-কেন্দ্ৰিক আলোড়নের ঐ পরিবেশে এই সময় অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে, ১৮৯৩ সালে, আমেরিকার চিকাগো শহরে বিখ্যাত বিশ্বধর্ম সম্মেলন বা ধর্ম মহা সভা অনুষ্ঠিত হয়,-স্বামী বিবেকানন্দের কারণে এবং প্রচারের গুণে যার সঙ্গে ভারতীয়, বিশেষত বাঙালীদের, একটি আবেগগত। সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। মিলেনারিয়ান আন্দোলন বা পরবর্তীকালের ফান্ডামেন্টালিজম’-এর সংকীর্ণ ও গোঁড়া মানসিকতা থেকে না হলেও এই ধর্মমহাসভার উদ্দেশ্য ছিল,-’একই সভায় বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বীদের প্রতিনিধিদের একত্রিত করে মত বিনিময় করা, বিভিন্ন খৃস্টান গোষ্ঠীদের সমন্বিত করা এবং পারস্পরিক সহানুভূতির সঙ্গে সবার কথা শোনা, জড়বাদীদের বিরুদ্ধে একটি ঐক্যবদ্ধ ধর্মীয় ফ্রন্ট’ গড়ে তোলা, বিশ্বের জন জীবনের উপর ধর্মের সুগভীর প্রভাব ব্যক্ত করা এবং বিভিন্ন দেশের ও ধর্মের মানুষের মধ্যে গ্ৰীতি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি। সম্মেলনের দু’বছর আগে থেকে জন ব্যারোজ-এর সভাপতিত্বে এই ধর্মমহাসভার জন্য কমিটি গড়া হয়েছিল; এর পক্ষ থেকে বিশ্বের নানা স্থানে যে চিঠি দেওয়া হয়েছিল তাতেই তার এই উদ্দেশ্যগুলি লেখা ছিল। স্পষ্টত এর মধ্যে মিলেনারিয়ানদের সংকীর্ণ বা মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গী ততটা ছিল না, যতটা ছিল। উদারনৈতিক কিন্তু নিছক ধর্মীয় অনুপ্রেরণা। এলাহাবাদের জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, কলকাতার হেবাবির্তনে ধর্মপাল, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও স্বামী বিবেকানন্দ সহ মোট ১৩ জন ভারতীয় প্রতিনিধি সশরীরে ঐ ধর্ম মহাসভায় উপস্থিত ছিলেন। মিলেনারিয়ান বা ফান্ডামেণ্টালিস্টদের মত বাইবেলের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য না থাকলেও, ঈশ্বরবিশ্বাসকে কেন্দ্র করে। গড়ে ওঠা ধর্মের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য তাঁদের অবশ্যই ছিল। এই উদ্দেশ্যের একটি সার্থক রূপায়ণ ঘটে স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে। এই ধর্মমহাসভায় ও তার পরেই তিনি হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায় নিরলস চেষ্টা করেন। কিছু সংস্কারমূলক, আপাত প্রগতিশীল, উদার ও কুসংস্কারমুক্ত কথাবার্তা মাঝে মাঝে বল্লেও, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ১৮৯৩-এর শিকাগো বক্তৃতার পরই বিবেকানন্দ কার্যত ঐক্যবদ্ধ, পেশীবহুল তথা জঙ্গী হিন্দুত্বের ভ্ৰাম্যমান দূতে পরিণত হন। এ কারণে এখনকার হিন্দু মৌলবাদীদের কাছে তিনি ও তাঁর কিছু সুবিধাজনক কথাবার্তা বেশ প্রিয়।)
ইভানজেলিক্যাল প্রোটেস্টান্টদের রক্ষণশীল গোঁড়া চিন্তার মধ্যে মিলেনারিয়ানদের প্রভাবের একটি উল্লেখযোগ্য বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯০২ সালে। এই সময় বাইবেলের প্রতি দ্বিধাহীন আনুগত্য ঘোষণাকারী অন্যান্য গোষ্ঠীদের সহযোগিতায় মিলেনারিয়ানরা ‘আমেরিকান বাইবেল লীগ’ প্রতিষ্ঠা করেন এবং ‘দি ফান্ডামেন্টালস’ নাম দিয়ে পরপর ১২টি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এই প্রথম ফান্ডামেন্টাল’ কথাটি একটি বিশেষ। ধর্মীয় তাৎপর্য বহন করে সাংগঠনিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু এই সব পুস্তিকার মধ্যেও তীব্র ঘূণা বা মনোরোগীসুলভ (hysterical) ধর্মীয় আবেগ ততটা ছিল না,-যা দেখা যায় এখনকার হিন্দু ও মুসলিম মৌলবাদীদের মধ্যে। তবে এগুলিতে বাইবেলকে পুন্যমূল্যায়ণ বা সমালোচনা করার তৎকালীন তত্ত্ব ও চিন্তাভাবনাগুলিকে আক্রমণ করা হয় এবং প্রিন্সটন সেমিনারীতে পাওয়া যুক্তির সাহায্যে বাইবেলের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়। বাইবেলের সমালোচনা ও আধুনিকতাকে যুক্তিতর্ক দিয়ে পর্যুদস্ত করার জন্য পূর্বসূরীরা যে প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন এই পুস্তিকাগুলি ছিল তারই সারসংক্ষেপ।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই অর্থাৎ ১৯১৪ সালের মধ্যে নায়াগ্রা সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা নেতৃবৃন্দের প্রায় সবাই মারা যান। নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব পূর্বসূরীদের মত আপন আদর্শে ততটা স্থির ছিলেন না, যতটা ছিলেন মিলেনারিয়ান মতাদর্শকে রক্ষণ করার ক্ষেত্রে আরো জঙ্গী ও আপোষহীন।
ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেই ঈশ্বরের প্রতিনিধি সম্পর্কিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রসঙ্গে মতবিরোধ প্রকাশ পাচ্ছিল। কিন্তু জেমস ব্রুকস বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীদের একত্রিত করে রাখতে পেরেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর কয়েকবছরের মধ্যেই নায়াগ্রা সম্মেলন বন্ধ করে দেওয়া হল এবং তার অল্প কিছু পরেই ‘ওয়াচওয়ার্ড অ্যাণ্ড টুথ’ ও ‘আওয়ার হোপ’ নামক দুটি মিলেনারিয়ান পত্রিকার মধ্যে কাগুজে লড়াই শুরু হয়ে গেল। এর ফলে মিলেনারিয়ান আন্দোলনে স্পষ্ট বিভেদ সৃষ্টি হয়। কিন্তু তার কাজ চলতেই থাকে।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ক্রমবর্ধমান উদারনীতিবাদ (Liberalism) ও ধর্মীয় সামাজিক অবক্ষয়ের ব্যাপকতায় সন্ত্রস্ত হয়ে মিলেনারিয়ানরা নিউ ইয়র্ক ও ফিলাডেলফিয়ায় সম্মেলন ও সমাবেশের আয়োজন করেন এবং এর ফলশ্রুতিতে, ১৯১৯ সালে ‘ওয়ার্লডুস। ক্রিশ্চিয়ান ফান্ডামেণ্টলস অ্যাসোসিয়েশন’ (World’s Christian Fundamentals Association) নামে একটি বৃহত্তর ও অধিকতর কার্যকরী সংগঠন সৃষ্টির পথ সুগম হয়। এর ফলে মিলেনারিয়ান আন্দোলন তার মূল চরিত্র না পাল্টে নামটি পাল্টায়। উপরন্তু ১৯১৯-এর এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে যে সাংগঠনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তার উপর। পরবর্তী তিরিশ বছর ধরে মিলেনারিয়ানফান্ডামেন্টালিস্ট আন্দোলন দাঁড়িয়ে থাকে। আমেরিকার ফান্ডামেণ্টালিজম মতবাদের তথা ফান্ডামেন্টালিস্টদের সংগঠিত রূপ ছিল এই অ্যাসোসিয়েশন। এখনকার মৌলবাদ-মৌলবাদী কথাগুলির সৃষ্টি ও ব্যবহারের পেছনে এরই অবদান সর্বাধিক।
আধুনিকতা (Modernism)-এর সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ লড়াই এই সময় থেকেই বিশেষ মাত্রা পায়। নেতৃবৃন্দ আন্দোলনের ধর্মীয় ভিত্তিকে বারংবার জোর দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে থাকেন, আধুনিকতা এবং তার সব ধরনের ‘অশুভদিক’কে (বিশেষত বিবর্তনবাদ-কে) বেঁটিয়ে বিদায় করার আহ্বান জানান। তারা বাস্তবত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে পরিহার করেন এবং সম্প্রতি প্রতিষ্ঠিত বাইবেল সংস্থায় (Bible Institutes-এ) তাঁদের আস্থা স্থাপন করেন। সব মিলিয়ে যেন মধ্যযুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইয়োরোপের ধর্মীয় কুসংস্কারকে বিংশশতাব্দীতে আমেরিকার বুকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা চলতে থাকে। (হিন্দু ও মুসলিম মৌলবাদীরা ভারত-বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশে বিংশশতাব্দীর শেষ পাদে যা করতে চাইছে।)
তখন আমেরিকায় ‘ফেডারেল কাউন্সিল অব চার্চেস অব দি ক্রাইস্ট’ (The Federa Council of Churches of the Christ) নামক ধর্মীয় সংগঠন ধর্মীয় ক্ষেত্রে ঐক্য, মিলন ও সহযোগিতার কথা বলছিল। এই নব্য ফান্ডামেন্টালিস্টরা তীব্রভাবে তারও বিরোধিতা করে এবং এই ধরনের আধ্যাত্মিক অবক্ষয়।’ চলতে থাকলে আলাদা হয়ে যাওয়ার হুমকি দিতে থাকে। (ভারতের হিন্দু মৌলবাদীরা যেমন এই ধরনের মানসিকতা থেকে মুসলিম তোষণ’-এর অভিযোগ এনে প্রতিক্রিয়াশীল। লড়াই চালাতে চাইছে)। কিন্তু মিনিয়াপলিস-এর ‘ফাস্ট ব্যাপটিস্ট চার্চ’-এর আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা (প্যাস্টর; pastor) ডব্লু. বি. রিলে (W. B. Riley), ব্যাপটিস্ট প্যাস্টর ও ইভানজেলিস্ট এ.সি. ডিক্সন (A. C. Dixon) এবং মুডি বাইবেল ইনস্টিটিউট’ (Moody Bible Institute)-এর অধ্যক্ষ, ইভানজেলিস্ট আর. এ. টোরি (R. A. Torrey)-র মত ব্যক্তিবর্গের জঙ্গী নেতৃত্ব সত্ত্বেও তাদের এই সংস্থার কখনোই এমন কিছু উন্নতি ঘটে নি।
ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আমেরিকায় গির্জা তথা ধর্মীয় পরিমণ্ডলে উদারপন্থী ব্যক্তির সংখ্যা ছিল নগণ্য,-তাদের অধিকাংশই ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় বা রোমান ক্যাথলিক যাজকদের শিক্ষণকেন্দ্ৰ (সেমিনারি)-র অধ্যাপক। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উন্নত সমালোচনাকে তাঁরা গ্রহণ করতেন। কিন্তু অধিকাংশ যাজক সম্প্রদায় ও ঐ ধরনের ব্যক্তিরা ব্যাপারটিকে আশঙ্কার চোখে দেখতেন। নব্য শিক্ষাকে খতিয়ে দেখার ক্ষেত্রে যেখানে আইনী ব্যবস্থা ছিল (যেমন প্রেসবিটরিয়ানদের মধ্যে), সেখানেই উদারপন্থীদের নতুন চিন্তাভাবনাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে, যেমন ঘটেছে বাইবেলীয় ঈশ্বরতাত্ত্বিক চার্লস এ. ব্রিগস (Charlis A. Briggs; Str8 S-SSSO) এর ক্ষেত্রে। কিন্তু কয়েক দশকের মধ্যেই এ ধরনের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের কৌশলগুলি ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত হয়, কারণ বাইবেলকে নতুনভাবে উপলব্ধি করার (তথা সমালোচনা করার) ব্যাপারটি মাথা চাড়া দিতে থাকে এবং নতুন প্রজন্মের ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তথা সেমিনারিগুলি উদারনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করতে থাকে। ১৯১৪ সালের মধ্যে উত্তরাঞ্চলের এপিস্কোপাল, মেথডিস্ট, ব্যাপটিস্ট ও প্রেসবিটেরিয়ানদের মত কিছু খৃস্টীয় গোষ্ঠীর মধ্যে উদারনীতি (Liberalism)-এর অনেক সমর্থক সৃষ্টি হয়। কিন্তু এই নতুন চিন্তাভাবনাকে প্রতিহত করার ও তার বিস্তার আটকানোর জন্য লড়াই করার অবস্থা তখন আর প্রায় ছিল না। ১৯২০ সাল নাগাদ শুধু এটুকু দেখা আর বাকি ছিল যে, এই উদারনৈতিকদের (Liberalsদের) সম্প্রদায় থেকে বের করা যায কিনা।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত পরোকার সময়ে আমেরিকানদের মধ্যে চরম অস্থিরতা, নৈরাশ্য, অসংযমী আচার-আচরণ ও সামাজিক নানা ধরনের ভীতির সৃষ্টি হয়েছিল। যুদ্ধের ফলে উদ্বেগ, হতাশা ও দুশ্চিস্তা আমেরিকাবাসীর বৃহদংশের মধ্যে ছড়িয়ে ‘ পড়ে। যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন, ব্যাপারটি এ চিত্রকে পাল্টাতে পারে নি। ইতিমধ্যেই আমেরিকায়, বিশেষত শ্রমিকদের মধ্যে, সাম্যবাদী মতাদর্শের প্রসার ঘটেছে এবং কম্যুনিষ্ট সংগঠন তৈরী হয়েছে। বিগত শতাব্দীতে বির্বতনবাদ যেমন প্রধানত ধর্মের ভিত্তি মূলে নাড়া দিয়েছিল, এখন এই সাম্যবাদ ধর্মীয়-সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বৈপ্লবিক রূপান্তরের সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হয়। এসবের প্রতিক্রিয়ায়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও বিদ্যালয়গুলিতেও ধর্মোপদেশের মধ্যে কম্যুনিজমএর প্রতি ভয়, শ্রমিক অসন্তোষ ও খুনজখম মারামারির ব্যাপারগুলি স্থান পায় ও আলোচিত হতে থাকে। আমেরিকার দ্বারা লীগ অব নেশনস ত্যাগ করার ঘটনায় এটি বোঝা যায় যে, বহু আমেরিকানই নতুন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে পছন্দ করে নি। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের ফান্ডামেন্টালিস্টদের মধ্যেও এই মানসিকতা ও কম্যুনিজম-এর প্রতি ভীতি ইত্যাদি অন্যান্য অনেকেরই মত ছিলই, কিন্তু ছিল আরো তীব্রভাবে, এবং ছিল পরিবর্তিত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নিজেদের বুদ্ধিবৃত্তিগত বিচ্ছিন্নতাবোধও।
তবে প্রোটেস্টাণ্ট সংগঠনের সর্বত্রই যে ১৯২০-এর সময় এ ধরনের বিতর্ক, বিরোধ বা দোদুল্যমানতা ছিল তা নয়। সাউদার্ন ব্যাপটিস্টদের মত কোন কোন সংস্থায় আধুনিকতা (Modernism) স্পষ্টভাবে দেখা দেয় নি; মেথডিস্ট ও এপিস্কোপাল চার্চে এর অনেক প্রভাব ছিল। কিন্তু পুরনোর সঙ্গে নতুনের দ্বন্দ্ব যথেষ্ট সংগঠিত হয় নি, সংস্থাগুলির সরকারী গঠনতন্ত্রও ব্যাপারটিকে সামনাসামনি আনার মত প্রচার চালানোর উপযোগী ছিল না।
কিন্তু নর্দার্ন ব্যাপটিস্ট সহ উত্তরাঞ্চলের রাজ্যগুলির প্রেসবিটেরিয়ানদের মধ্যে গুরুতর বিতর্ক সৃষ্টি হয়। প্রেসবিটেরিয়ান চার্চের মধ্যে যে রক্ষণশীল গোঁড়া অংশে প্রিন্সটন সেমিনারীর ঈশ্বরতাত্ত্বিক অবস্থান প্রতিফলিত হয়, তারা মিলেনারিয়ানদের সাহায্য নিয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মতবাদ রচনা করে এবং ১৯১০-এ যে অবস্থান ছিল তার সঙ্গে যুক্ত করে, তারা বলে যে, খৃস্টান ধর্মে বিশ্বাসী হতে হলে কয়েকটি দিককে অবশ্যই গ্ৰহণ করতে ও বিশ্বাস করতে হবে, যেমন, (১) বাইবেলের অবিসংবাদিত কর্তৃত্ব ও প্রেরণা, (২) কুমারী মায়ের থেকে খৃস্টের জন্ম (the virgin birth of Christ), (3) প্রায়শ্চিত্ত করা ও এর জন্য অনুষ্ঠানাদি, (8) পুনরভ্যুত্থান (resurrection) এবং (৫) যিশু খৃস্টের ঐশ্বরিক অলৌকিক ক্ষমতা। ১৯২২ সালে হ্যাঁরি এমারসন ফসডিক (Harry Emerson Fosdick) নামে নিউইয়র্কের এক যাজক মডানিস্ট-দের একজন প্রথম সারির মুখপাত্র হয়ে ওঠেন এবং বিদেশে মিশনারীদের কর্মক্ষেত্রে মিলেনারিয়ানদের কিছু কাজকর্মের (যেমন ফান্ডামেন্টালিস্টরা কি জিতবো?’ এমন শিরোনামে ধর্মোপদেশ দেওয়া) প্রতিবাদ করেন। কিন্তু এর ফলে ‘ফাস্ট প্রেসবিটেরিয়ান চর্চ’-এর প্যাস্টর-এর পদ থেকে, ব্যাপটিস্ট ফসডিক-কে রক্ষণশীলেরা ও মিলেনারিয়ানরা মিলে সরিয়ে দিতে সক্ষম হয়।
জেমস এইচ ব্রুকস (James H. Brookes)-এর মত মিলেনারিয়ানরা এবং প্রিন্সটন অধ্যাপক জে. গ্রেশাম মাচেন (J. Gresham Machen)-এর মত রক্ষণশীলেরা চাইছিলেন যাতে উদারনৈতিকেরা নিজে থেকেই সরে যায়। আমেরিকার প্রেসবিটরিয়ান চার্চের মধ্যে বিভাজন আটকাতে সমঝোতার একটি রাস্তা বের করানোর জন্য ১৫ জনের একটি কমিশন (Commission of Fifteen) নিয়োগ করা হয়। এঁরা রিপোর্ট দেন যে, প্রেসবিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের মধ্যে মতামতের বৈচিত্র্যাকে সহ্য করার ঐতিহ্য রয়েছে। খৃস্টান ধর্মে বিশ্বাসের অত্যাবশ্যক দিকগুলি কি তা ঠিক করার জন্য সাধারণ সভাকে ক্ষমতা দেওয়ার ব্যাপারটিকেও তারা বাতিল কদের দেন। এর ফলে প্রধানত রক্ষণশীলদের অবস্থান ধ্বসে যায়। নর্দার্ন ব্যাপটিস্টদের অভ্যস্তরীণ বিরোধ তাদের বাৎসরিক সভায় প্রকাশ্যে আসে, যেটি একটি দলীয় রাজনৈতিক সভার চেহারা নিয়েছিল। ১৯২০ সাল থেকে ব্যাপটিস্টদের একটি গোষ্ঠী নিজেদের ‘ন্যাশন্যাল ফেডারেশান অব ফান্ডামেন্টালিস্টস’ (National Federation of Fundamentalists; মৌলবাদীদের জাতীয় জোট) নামে অভিহিত করতে থাকে। মৌল ব্যাপটিস্ট নীতির উপর এরা বাৎসরিক সভার অব্যবহিত পূর্বে সম্মেলনের আয়োজন করতে শুরু করে, এইভাবে সংগঠিত হয়ে নিজেদের মতামতকে তারা মূল সভায় নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালায়। ‘ন্যাশনাল ফেডারেশান অব ফান্ডামেন্টালিস্টস’-এর এ ধরনের কৌশল খুব একটা কাজ দেয় নি; এর ফলে আরো কিছু জঙ্গী ব্যাপটিস্ট ফান্ডামেন্টালিস্টরা ‘ব্যাপটিস্ট বাইবিল ইউনিয়ন।’ (Baptist Bible Union) গড়ে তোলে। কিন্তু প্রেসবিটেরিয়ানদের মত ব্যাপটিস্টদের মধ্যেও ফান্ডামেন্টালিস্টদের নিজেদের মধ্যেকার বিভাজন তাদের পরাজয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
ক্রমবর্ধমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ তথা ধর্মের ক্রমশঃ প্রমাণিত অপ্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদির ফলে রক্ষণশীল গোঁড়ারা শামুকের মত মৌলবাদের আশ্রয় নেয় অর্থাৎ নতুনকে জোর করে অস্বীকার করে প্রাচীনকে আঁকড়ে রাখে। আমেরিকার ফান্ডামেন্টালিস্টরা ছিল। এরই আধুনিক সাংগঠনিক রূপ। ইয়োরোপের মধ্যযুগে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে এমন বাইবেল-বিরোধী। কিন্তু সত্যি কথা বলার জন্য কত মনীষী ও বিজ্ঞানীকে লাঞ্ছিত করা হয়েছে, এমনকি হত্যাও করা হয়েছে। একই মানসিকতা থেকে এই বিংশ শতাব্দীর শুরুতে, ১৯২০ সাল নাগাদ, বিবর্তনবাদ (evolution)-এর শিক্ষায় রুষ্ট হয়ে, বাইবেলের সমালোচনায় উদ্বিগ্ন হয়ে, আমেরিকায় ফান্ডামেন্টালিস্টরা জঙ্গী আন্দোলন শুরু করে। তারা মনে করত যে, চার্লস ডারউইন যে বিবর্তনবাদের তত্ত্ব উপস্থিত করেছেন তার সঙ্গে বাইবেলের শিক্ষা খাপ খায় না, তাই তারা বিবর্তনবাদের বিরোধিতা করে। কিন্তু মজার ব্যাপার ও লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যাঁরাই বিবর্তনবাদের বিরোধিতা করতেন তারা সবাই যে ফান্ডামেন্টালিস্ট ছিলেন তা নয়। বিবর্তনবাদ-বিরোধী ‘যোদ্ধারা’ সরকারী স্কুলে বিবর্তনবাদ না পড়ানোর জন্য আইনপ্রণয়ন করতে প্রচার চালায়। টেনেসি (Tennesse)-তে এ ধরনের আইনও হয়ে যায়। অবশ্য পরে, ১৯২৫-এ, আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন (ACLU)-এর উদ্যোগে আদালতে এটিকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়। ছোট্ট শহর ডেটন’ (Dayton)-এর জন টি. স্কোপিস (John T. Scopes) নামে এক বিজ্ঞান-শিক্ষক বিবর্তনবাদ পড়ানোর অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হিসেবে সাক্ষ্য দিতে এগিয়ে আসেন। ঐ দশকের দুই বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব, প্রেসবিটেরিয়ান ফান্ডামেন্টালিস্ট উইলিয়াম জেনিংস (William Jennings) ও বিখ্যাত মামলাগুলিতে প্রতিবাদী পক্ষের নামকরা উকিল ক্ল্যারেন্স ড্যারো (Clarence Darrow) ঐ সময় এই মামলায় সংবাদের শিরোনামে আসেন; প্রথম জনের ভূমিকা ছিল মামলা রুজু করে বাদী পক্ষের সহকারী অ্যাটর্নির এবং দ্বিতীয় জন ছিলেন প্রতিবাদী পক্ষের অ্যাটর্নি।
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আমেরিকা থেকে বহুদূরে, ভারতীয় ভূখণ্ডেও মোটামুটি এই সময়কালেই হিন্দু মৌলবাদেরও তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। কুড়ির দশকের মাঝামাঝি, একদা ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামী বীর সাভারকর হিন্দুত্বের প্রধান তাত্ত্বিক প্রবক্তা ও হিন্দু মহাসভার নেতারূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ১৯২৩এ প্রকাশিত হয় তঁর ‘হিন্দুত্ব! হিন্দু কে?’ পুস্তিকাটি। আর ১৯২৫-এর বিজয়া দশমীর দিন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আর এস এস) প্রতিষ্ঠা করেন ডঃ হেডগেওয়ার ও তার অন্য পাঁচজন বন্ধু। উল্লেখযোগ্য যে, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, ভারতীয় জনতা পার্টি (বি জে পি), বজরং দল, ভারতীয় মজদুর সংঘ বা অখিল ভারতীয় বিদ্যাথী পরিষদ হিন্দু রাষ্ট্রের ধারণার মূল চালিকাশক্তি নয়; এর মূল চালিকাশক্তি এই আর এস এস-ই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরোকার অর্থনৈতিক সামাজিক ব্যবস্থা এবং একই সঙ্গে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রতিক্রিয়া—এগুলি এক্ষেত্রেও ভূমিকা পালন করেছিল।
অন্যদিকে ১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে আমেরিকার ফান্ডামেন্টালিস্টরা সংঘাতের জায়গা থেকে সরে আসে এবং জাতীয় ক্ষেত্রেও তারা আর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে থাকে না। এই সময়কালে যান্ত্রিকভাবে ও কঠোরভাবে সংযত নৈতিক জীবনযাপনকে একটি দার্শনিক ভিত্তি দেওয়া হয়। ভোগসর্বস্বতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, বিলাসব্যসন থেকে দূরে থাকার, এমন কি নাচগান করা, সিনেমা নাটক দেখা বা মদ্যপানধূমপান করা ইত্যাদির বিরুদ্ধেও তাঁরা তীব্র প্রচার শুরু করেন। এই সময়েই আধুনিক ফান্ডামেন্টালিজম-এর প্রতিষ্ঠানিক রূপ বিকশিত হতে থাকে, (যা এখনো আমেরিকায় নানাভাবে এবং ভালভাবেই আছে)। কিছু ফান্ডামেন্টালিস্ট তাদের সংগঠন থেকে বেরিয়ে এসে নতুন চার্চ প্রতিষ্ঠা করেন যেমন জেমস জে মাচেন (James J. Machen)-এর নেতৃত্বে কিছু প্রেসবিটেরিয়ান ‘প্রেসবিটেরিয়ান চার্চ ইন আমেরিকা’ বা ‘নির্দান ব্যাপটিস্ট কনভেনশান’ ছেড়ে কিছু ব্যাপটিস্ট ‘জেনারেল অ্যাসোসিয়েশন অব রেগুলার ব্যাপটিস্টস’ গড়ে তোলেন। কিন্তু অধিকাংশ ফান্ডামেন্টালিস্টরাই এক একটি ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠীতে জড়ো হন, যেগুলি সর্বতোভাবে বাইবেলের আক্ষরিক অনুসরণে এবং মিলেনারিয়ানের পূর্ববর্তী অবস্থানের প্রতি বিশ্বস্ত, যেমন ‘খুষ্টান অ্যান্ড মিশনারী অ্যালয়েন্স’, ‘প্লাইমাউথ বৃন্দ্রেন’, ‘ইভানজেলিক্যাল ফ্রি চার্চ কিংবা ঐ সময় গড়ে ওঠা অজস্র স্বাধীন ‘বাইবেল চার্চ’ ও উপাসনাকেন্দ্রের কোন কোনটিতে।
বর্তমানে আমেরিকায় ফান্ডামেন্টালিজম এইভাবে রূপান্তরের পর নানান ক্ষেত্রে টিকে আছে। এই আধুনিক ফান্ডামেন্টালিজম (modern Fundamentalism) তার সাংগঠনিক রূপের অনেকটাই ‘বাইবেল ইনস্টিটিউট’ ও ‘বাইবেল কলেজগুলি থেকে পেয়েছে। চিকাগোর ‘মুডি বাইবেল ইনস্টিটিউট’ (Moody Bible Institute) বা লস এঞ্জেলস-এর বাইবেল ইনস্টিটিউট’-এর মত এ ধরনের অনেক শিক্ষাকেন্দ্ৰে শুধু ছাত্রদের পড়ানোই হয় না, তারা তাদের নিজস্ব পত্রিকা প্রকাশ করে, নিজেদের বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচার চালায়, সভা-সম্মেলনের আয়োজন করে এবং সংগঠন বাড়ানোর জন্য বক্তাদের মাইনে পাওয়া কৰ্মচারী হিসেবেও রাখে। মূল সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ কেন্দ্রের মতই তারা সংগঠন চালায় এবং এইভাবে প্রায় সমমনোভাবাপন্ন কিন্তু পরস্পরবিচ্ছিন্ন সংস্থাগুলির মধ্যে একটি যোগসূত্র বজায় রাখে। চিকাগোর শহরতলী এলাকায় এই ধরনের জ্ঞানচর্চার নামকরা কেন্দ্ৰ, হুইটন কলেজ, দীর্ঘদিন ধরে শিল্প ও বিজ্ঞানের সবচেয়ে শক্তিশালী দুর্গ হিসেবে কাজ করেছে।
আমেরিকার সমাজের ব্যবসায়িক ও পেশাগত বিভিন্ন সংস্থার পাশাপাশি, ও প্রায় সমকক্ষ হিসেবে, ফান্ডামেন্টালিস্টদেরও বহু সংস্থা রয়েছে। ছাত্র, নার্স, ডাক্তার, বিজ্ঞানী, ক্রীড়াবিদ, সমাজকর্মী, ঐতিহাসিক, ব্যবসায়ী ও অন্যান্যরা তাঁদের নিজস্ব স্বাৰ্থবাহী বা প্ৰশিক্ষণের জন্য গড়া এ ধরনের আপনি আপন সংস্থায় যোগ দিতে পারেন। বৃহৎ প্রোটেস্টান্ট সংগঠন ও রোমান ক্যাথলিকদের মত, শত শত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এঁদেরও নিজস্ব ‘ক্যাম্পাস ক্রুসেড ফর ক্রাইস্ট’ ও ‘ইন্টার-ভার্সিটি ক্রিস্টিয়ান ফেলোশিপ’,ইত্যাদি রয়েছে। এদেরই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ‘আমেরিকান সায়েন্টিস্ট অ্যাফিলিয়েশন’ নিয়মিত আলোচনাসভায় বসেন এবং একটি পত্রিকা প্ৰকাশ করেন; এই পত্রিকায় বিজ্ঞানের সঙ্গে বাইবেল ও খৃস্টান বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী কিভাবে একসঙ্গে পাশাপাশি মানিয়ে থাকতে পারে তার উপর জোর দেওয়া হয়।
প্রোটেস্টান্ট মতের বৃহৎ সংস্থাদির সমকক্ষ হিসেবে ফান্ডামেন্টালিস্টদের দ্বারা প্রভাবিত ‘অ্যামেরিকান কাউন্সিল অব ক্রিস্টিয়ান চার্চেস’ (ACCC; প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৪১) ও ‘ন্যাশন্যাল অ্যাসোসিয়েশন অব ইভানজেলিক্যিাল’ (NAE; প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৪২) রয়েছে। ১৯৬৯ অবিদ প্রথমোক্ত সংস্থাটি বাস্তবত ক্যাল ম্যাকআনটায়ার (Carl McIntire) নামে একজন ব্যক্তিরই মুখপাত্র ছিল। ন্যাশন্যাল কাউন্সিল অব চার্চেস-এর মত বৃহত্তর খৃস্টান সংগঠনের বিরুদ্ধে এবং আমেরিকাকে ধ্বংস করার জন্য কম্যুনিস্ট, ষড়যন্ত্রের বিপদের বিরুেদ্ধে ইনি প্রচার চালাতেন। দ্বিতীয়োক্ত সংস্থাটি তার সদস্যদের মধ্যে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে কিন্তু নিজস্ব কোন কর্মসূচীর রূপায়ণ করে না।
যুদ্ধের পরবর্তী দশকগুলিতে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, ১৯৫০-এর ধর্মীয় পুনরভ্যুত্থান এবং কম্যুনিস্টরা সব গণ্ডগোল করে দেবে এমন ভয় ও অভিযোগ–এই বিষয়গুলি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে আমেরিকায় ফান্ডামেন্টালিস্ট ও ইভানজেলিক্যাল চার্চের উপর সবচেয়ে বেশি ও গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। এই সময়ে ফান্ডামেন্টালিস্টদের নতুন এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, বিখ্যাত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিটি যথাসম্ভব ছিলেন ইভানজেলিস্ট বিলি গ্রাহাম (Billy Graham) (জন্ম-৭.১১.১৮; ভিন্ন নাম-উইলিয়াম ফ্র্যাংলিন গ্রাহাম)।
১৯৫০ সাল নাগাদ ইনি ছিলেন ফান্ডামেন্টালিস্টদের প্রধান মুখপাত্র। ফান্ডামেন্টালিস্ট তথা ধর্মীয় মৌলবাদীদের সঙ্গে শাসকশ্রেণীর আঁতাতের জুলন্ত উদাহরণ ছিলেন ইনি। ১৯৪৯ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হ্যাঁরি এস. ট্রম্যান। এঁকে প্রথম হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ করে আনেন। পরে সেখানে তার অবাধ যাতায়াত শুরু হয়। ডুইট ডি, আইসেনহাওয়ার, লিন্ডন জনসন ও রিচার্ড এস. নিক্সনের মত আমেরিকার পরবর্তী প্রেসিডেন্টদের ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত বন্ধু এবং গলফ খেলার সঙ্গী হয়ে উঠেছিলেন এই বিলি গ্রাহাম। জোনস কলেজে (ক্লিভল্যান্ড, টেনেসি) ও ফ্লোরিডা বাইবেল ইনস্টিটিউট (ট্যাম্পার নিকটবতী) নামে ফান্ডামেন্টালিস্টদের দুটি প্রতিষ্ঠানে ইনি পড়াশুনা করেন এবং শেষেরটি থেকে ১৯৪০-এ স্নাতক হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইলিনয়েসের হুইটন কলেজ থেকে নৃতত্ত্বে বি.এ. ডিগ্রি অর্জন করেন। ক্রুসেড নাম দিয়ে বহু প্রচারমূলক ভ্ৰমণ করার পাশাপাশি, ‘বিলি গ্রাহাম ইভানজেলিস্টিক অ্যাসোসিয়েশন’ প্ৰতিষ্ঠা করেন। নিজের ধর্মীয় প্রচারগুলিকে ‘ডিসিসান’ নামে পত্রিকা প্রকাশ করে ও অন্যান্য লেখাপত্রের মধ্য দিয়ে প্রচার করেন।
কম্যুনিজমের ভয় এই ১৯৫০-এর সময়কালে আমেরিকায় একটি বিরাট গণ বিতর্ক ও বাদ প্রতিবাদের বিষয় ছিল। এর জন্য বহু সংস্থায় ভাঙ্গনও ঘটে গেছে। আমেরিকার শাসকশ্রেণী ও ফান্ডামেন্টালিস্ট-উভয়ের কাছেই এই কমিউনিজম ছিল প্রধান শত্রু ও প্রবল ভীতিপ্রদ, প্রতিরোধযোগ্য ব্যাপার। কম্যুনিজমের প্রতি এই ভয়ের ব্যাপারটার সঙ্গে ফান্ডামেন্টালিস্টদের চিরাচরিত শত্রুর (অর্থাৎ বাইবেলের সমালোচনা ও বিবর্তনবাদ) চরিত্রগত কিছু মিল রয়েছে, যেমন এটি (কমিউনিজম) বাইরে থেকে এসেছে, এমনভাবে তা ছড়িয়ে পড়ছে যে মনে হচ্ছে তাকে আটকানো যাবে না। আর সবকিছু ওলোট পালট করে দেবে এবং সেটি খৃস্টধর্মকে বেশ হতমোনই করছে। বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তীকালের এই কম্যুনিস্ট-বিরোধী ধৰ্মযুদ্ধ যেন ১৯২০এর বির্বতনবাদ-বিরোধী ধর্মযুদ্ধেরই হুবহু পুনরাবৃত্তি।
সত্তর-এর দশকের শেষের দিকে বিবর্তনবাদ নিয়ে বিতর্ক আবার মাথা চাড়া দেয়। এই সময়কালের মধ্যে বিবর্তনবাদ একটি বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে গৃহীত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কিন্তু তথাকথিত সৃষ্টিবাদীরা (Creationists) স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রমে বাইবেলের সৃষ্টি সৃষ্টি কাহিনী (Biblical Creation account)-কে অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানাতে থাকে এবং তার জন্য প্রচার আন্দোলন চালায়। রক্ষণশীল ক্ষেত্রগুলিতে এর ফলে ফান্ডামেন্টালিস্ট সৃষ্টিবাদীরা কিছু জমি খুঁজে যায়। নিজের ছেলেমেয়েদের কি পড়ানো হবে বা হচ্ছে, তা ঠিক করার অধিকার বাবা-মায়েরও থাকা উচিত। কিনা,—এ ধরনের বৃহত্তর বিতর্কও এর ফলে সৃষ্টি হয়।
আর ৭০-এর দশকের শেষের দিকের এই সময়কালেই তথাকথিত মরাল মেজরিটি, (Moral Majority) নামে ফান্ডামেন্টালিস্ট নাগরিকদের একটি সংস্থা ধৰ্মযুদ্ধে নামে। এর নেতৃত্ব দেন ভার্জিনিয়ার ব্যাপটিস্ট যাজক জেরি ফ্যালওয়েল (Jerry Falwell)। বাইবেলের কর্তৃত্বের প্রতি আগেকার আপোষহীন মানসিকতার সঙ্গে গর্ভপাত, সমলিঙ্গী যৌন অধিকার, সমানাধিকার সম্পর্কিত আইনের সংশোধন—এ সবের বিরুদ্ধে এবং স্কুলে প্রার্থনাসভার আয়োজন করা, প্রতিরক্ষণ খাতে ব্যয় বাড়ানো, কম্যুনিস্ট বিরোধী বৈদেশিক নীতিকে শক্তিশালী করা, —এসবের স্বপক্ষে এই ফান্ডামেন্টালিস্টরা আন্দোলন গড়ে তোলে। মৌলবাদী বলতে এখন যাদের বোঝানো হচ্ছে, তাদের সঙ্গে এই মরাল মেজরিটি-র সাদৃশ্যই সবচেয়ে সাম্প্রতিক। ভারতের হিন্দুমৌলবাদীরা বা কিছু ইসলামী দেশের মুসলিম মৌলবাদীরা প্রায় হুবহু একই ধরনের দাবী এখন জানাচ্ছে-হিন্দু-মুসলিম সবার জন্য একই আইন থেকে কঠোর কম্যুনিষ্ট বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী আদি।
এখনো আমেরিকায় টিকে থাকা ফান্ডামেন্টালিস্টদের বিশ্বাস সেই নায়াগ্রা সম্মেলনের সময় থেকে এমন কিছু পাল্টীয় নি। এখনকার ফান্ডামেন্টালিস্টরা ধূমপান বা মদ্যপান না করা, নাটকে অংশগ্ৰহণ না করা জাতীয় নানা ধরনের আচরণবিধি অনুসরণ করেন। এ সম্পর্কে গোঁড়ার দিকেই বলা হয়েছে। এটিও উল্লেখ্য যে, সম্প্রতিকালে আধুনিক ফান্ডামেন্টালিজমের ইতিহাসে সবচেয়ে উত্তেজনাকর আধ্যাত্মিক তথা ঈশ্বরতাত্ত্বিক (theological) আলোড়ন ঘটে কার্ল বার্থ (Karl Barth)-এর ঈশ্বরতত্ত্ব সম্পর্কিত ব্যাখ্যায়। তিনি বাইবেলের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বকে কঠোরভাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। এবং এটি ফান্ডামেন্টালিস্ট দৃষ্টিভঙ্গীরই প্রতিফলন বলে অনেকে মনে করেন।
[কার্লবাৰ্থ (জন্ম সুইজারল্যান্ডের বাসেল-এ, ১০ই মে, ১৮৮৬; মৃত্যু-৯ বা ১০ই ডিসেম্বর, ১৯৬৮)-একদিকে নাৎসি-বিরোধী ও জাতীয় সমাজতন্ত্র’ (National Socialism)-বিরোধী কাজের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন, অন্যদিকে ছিলেন প্রোটেস্টান্ট চিন্তায় মৌলিক পরিবর্তন আনার প্রসঙ্গে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব। ঊনবিংশ শতাব্দীর উদার ঈশ্বরতত্ত্ব (liberal theology) ঈশ্বরকে মানুষের মত, মানুষের কাছাকাছি এনে (anthropocentrism) হাজির করছিল। এর বিরুদ্ধে কার্ল বার্থ ঈশ্বরের পরিপূর্ণ অনন্যতা (Wholy Otherness of God)–র উপর জোর দেন। সুইজারল্যান্ড থেকে ইনি আমেরিকায় যান। ১৯৬২ সালে। চার্চ ডগম্যাটিকস’ নামে এর লেখা সুবৃহৎ গ্রন্থ আছে। বাইবেল সহ যিশুখৃস্ট সম্পর্কে কোন ধরনের দ্বিধা, অবিশ্বাস, সমালোচনা বা তর্কবিতর্ককে পরিপূর্ণভাবে পরিহার করে তাঁর দ্বিধাহীন ঘোষণা ছিল,–‘…Jesus Christ, as He is attested for us in Holy Scripture, is the one Word of God, which we have to hear and which we have to trust and obey in life and in death.’]
আমেরিকায় সৃষ্টি হওয়া ও টিকে থাকা এই ফান্ডামেন্টালিজম ও ফান্ডামেন্টালিস্টদের মানসিকতা ও ক্রিয়াকান্ডের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকার কারণেই আমাদের দেশে সম্প্রতি মৌলবাদ ও মৌলবাদীর মত ‘আধুনিক পরিভাষা’-র সৃষ্টি হয়েছে। এবং সাম্প্রতিক মৌলবাদীরা ফান্ডামেন্টালিজমের আধুনিকীকরণ করেছে। হিংসা, জঙ্গীপনা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের আকাঙক্ষা-এগুলিকে তার সঙ্গে সংযুক্ত করে। কথাগুলির তাৎপর্য শুধু আমেরিকা বা ভারত বলে নয়, আন্তর্জাতিক ভাবেই তার সাধারণীকরণ ঘটেছে, পেয়েছে কিছু নতুনতর মাত্রাও।
৩. মৌলবাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
Fundamentalis ও মৌলবাদের অন্যতম দুটি আভিধানিক অর্থের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে, এগুলি হল যথাক্রমে, ‘বাইবেল বা অন্য ধর্মশাস্ত্রের বিজ্ঞানবিরুদ্ধ উক্তিতেও অন্ধবিশ্বাস’ এবং ‘ধর্মীয় গোঁড়ামির ফলে জাত সংকীর্ণ মতবাদ’। এ ধরনের সংজ্ঞা থেকে মৌলবাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি দিক স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, যেমন তা ধর্মের সঙ্গে (অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানিক ধর্মের সঙ্গে) সংশ্লিষ্ট, ধর্মান্ধতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামি তার সম্পৃক্ত দিক, এটি একটি বিজ্ঞানবিরুদ্ধ ও সংকীর্ণ চিন্তা। স্পষ্টতঃই মানুষের চেতনা ও সমাজের উত্তরণের বিরোধী এটি এবং যাদের মধ্যে এই অন্ধবিশ্বাস, গোঁড়ামি, বিজ্ঞানবিরুদ্ধতা ও সংকীর্ণতা দেখা যায়, তাদেরই সাধারণভাবে মৌলবাদী বলা যায়।
Fundamental কথাটিরও অর্থ ‘আদিম’ বা ‘মূল’। মৌলবাদ কথার ভাবগত অর্থ তাই মূল বা শিকড়ে ফিরে যাওয়ার তত্ত্ব। কথাটি এখন সাধারণভাবে ব্যাপক ব্যবহৃত হতে হতে একটি নিন্দাসূচক কথায় পরিণত হলেও, এই শিকড়ে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা মানুষের কমবেশি থাকেই। অ্যালেক্স হেলির বিখ্যাত বই ‘The Root’ (বাংলা অনুবাদ-‘শেকড়ের সন্ধানে’) এই প্রবণতারই ফসল। কিন্তু তা মৌলবাদ নয়। নিজের অতীতকে জানা, নিজ ধর্মীয় বা রাজনৈতিক গোষ্ঠীর প্রথমদিকের ইতিহাস জানা তথা নিজের উৎস সম্পর্কে আগ্রহ বরং একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ও মানবিক ইতিবাচক লক্ষণ। কিন্তু যখন তা তত্ত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ঐ আদিম প্রাচীন মূল দিকেই ফিরে যাওয়ার কথা অন্ধভাবে বিশ্বাস করা ও করানো হয় অর্থাৎ পরিবর্তিত পরিবেশ-পরিস্থিতি জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ঐ মৌলিক আদিমতার পরিমার্জনা ও রূপান্তরকে অস্বীকার করা হয় তখন তা মৌলবাদ বা মৌলবাদী তত্ত্বে পরিণত হয়। এর সঙ্গে পরমত-অসহিষ্ণুতা, নিজেদের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবা, এই তত্ত্বকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের সংকীর্ণস্বার্থ সিদ্ধি করা এবং তার জন্য অনৈতিহাসিক মিথ্যাচারের সঙ্গে হিংস্ৰ উগ্ৰ অন্ধ আচরণ করা-ইত্যাদিও মিশে থাকে। এটি অবশ্যই মানুষ ও তার সভ্যতার বিরোধী। এটি প্রগতি ও বিকাশের পথ রোধ করে। বাইবেল ও যিশুকে অভ্রান্ত ধরা, কোরাণকে হুবহু অনুসরণ করার কথা ভাবা, হিন্দুধর্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভেবে হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা—ইত্যাদি এরই ফসল। এইভাবে বিশেষ কোন প্ৰতিষ্ঠানিক ধর্মকে কেন্দ্র করে সাধারণতঃ মৌলবাদ তথা ধর্মীয় মৌলবাদ সৃষ্টি হলেও, কোন রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক তত্ত্ব কিংবা বিশেষ কোন মতাদর্শে অন্ধ গোঁড়া উগ্ৰ বিশ্বাসও মৌলবাদী মানসিকতারই বিশেষ রূপ।
আমেরিকায় প্রতিষ্ঠানিক ভাবে সৃষ্টি হওয়া Fundamentalism-এর পূর্ববর্তী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে এর কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকৰ্ষিত হয়। যেমন
(১) এটি অবশ্যই ধর্মের সঙ্গে সম্পূক্তভাবে যুক্ত। প্রতিষ্ঠানিক একটি ধর্মে (এখানে খৃস্টধর্মে) বিশ্বাস তার প্রাথমিক ভিত্তি। তাকে আরো গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত করাই তার লক্ষ্য।
(২) এটি আসল প্রতিষ্ঠানিক ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থকে (তথা মৌলিক প্রাথমিক দিকগুলিকে) অপরিবর্তনীয়, সমালোচনার উদ্ধেৰ্ব, সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধিকারী হিসেবে মনে করে এবং এই মনে করার মধ্যে কোন আপোষ করতে সে প্রস্তুত নয়। এ কারণে তার কাজের মধ্যেও ধর্মান্ধিতার স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং Fundamentalism বা মৌলবাদ নামটি এ কারণেই হয়েছে।
(৩) কোন নতুন ধরনের বৈজ্ঞানিক চিন্তা, —তা সে বির্বতনবাদ থেকে সাম্যবাদ বা কম্যুনিজম যাই-ই হোক না কেন, যা ঐ ধর্ম তথা ধর্মগ্রন্থের ভিত্তিমূলে নাড়া দিতে চায়, তার প্রতিক্রিয়ায় তার জন্ম ও তার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামে সে কঁাপিয়ে পড়ে। এক কথায় যুক্তিবোধ ও বিজ্ঞানমনস্কতাকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করেই তার সৃষ্টি ও টিকে থাকা। এটি চূড়ান্তভাবে অবৈজ্ঞানিক ও প্রতিক্রিয়াশীল।
(৪) ধর্মীয় ক্ষেত্রেও উদারনীতি, আধুনিকতা ও ভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রতি সহিষ্ণুতা-এ সবেরও সেটি বিরোধী। তাই ধর্মীয় সংকীর্ণতা তার কাজকর্মের মধ্যে প্রকাশ পায়।
(৫) কিছু প্রতিষ্ঠানিক ধর্মের সৃষ্টি তথা ধর্মীয় আন্দোলন মানুষের সমাজইতিহাসের বিশেষ পর্যায়ে তার অগ্রগমন ও সংস্কারের পথ সুগম করলেও ফান্ডামেন্টালিজম-এর ক্রিয়াকান্ডের মধ্যে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার, এমনকি পশ্চাদগমনের আকাঙক্ষারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে।
এখন থেকে আড়াই হাজার বছর আগে বৌদ্ধ বা জৈনধর্মের, দু’হাজার বছর আগে খৃস্টধর্মের, দেড়হাজার বছর আগে ইসলাম ধর্মের বা পাঁচশ’ বছর আগে শিখধর্মের সৃষ্টি, এমনকি হিন্দুধর্মের মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম, ভক্তি আন্দোলন বা বৈষ্ণবধর্ম ইত্যাদির সৃষ্টি এবং খৃস্টধর্মে প্রোটেস্টান্টিজমের জন্ম ইত্যাদির মধ্যে তখনকার ধর্মীয় আবিলতা, সামাজিক অবক্ষয় ও অনাচার, সামাজিক পীড়ন ও শোষণ, ইত্যাদির বিরুদ্ধে মানুষের লড়াই রূপ পেয়েছিল। ঈশ্বর বিশ্বাস বা বিশেষ ধর্মীয় আধ্যাত্মিক বিশ্বাসকে অবলম্বন করে বিশেষ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তার নেতৃত্ব দিলেও, ধর্ম ও সমাজের প্রসঙ্গে সেগুলির ইতিবাচক কিছু সংস্কারমূলক দিকও ছিল। কিন্তু বিগত শতাব্দীতে এই যে ফান্ডামেন্টালিজম নামে সংগঠিত ধর্মীয় আন্দোলন শুরু হয়েছিল, যার অবশেষ এখনো আছে এবং ভারতসহ নানা দেশে ভিন্ন পরিবেশে যা মূলত একই চরিত্র নিয়ে আরো উগ্রভাবে মাথা চাড়া দিয়েছে, তার মধ্যে ঐ ধরনের কোন ইতিবাচক দিক আবিষ্কার করা দুরূহ। বরং তা প্রগতিশীল সংস্কারইচ্ছার বা বৈপ্লবিক প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করতে তার প্রতিক্রিয়াতেই জন্মলাভ করছে।
(৬) দ্বিধাহীন বিশ্বাস ও প্রশ্নহীন আনুগত্য তথা চূড়ান্ত কর্তৃত্ববাদ তার অন্যতম সম্পূক্ত দিক। প্রাচীন ধর্মীয় অনুশাসন ও ধর্মগ্রন্থগুলিকে নিজেরা তো প্রশ্ন করেই না, অন্য কেউ তার চেষ্টা করলেও তাকে শত্রু হিসেবে গণ্য করতে থাকে। কেন পরিবর্তিত পরিবেশ পরিস্থিতি ও উন্নততর জ্ঞানের আলোয় তাদের বিচার করা যাবে না, ‘পাপ’ করলে ‘প্ৰায়শ্চিত্ত’ নামক কিছু মনগড়া ধর্মীয় অনুষ্ঠান করলে সব অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কিনা, কোন মেয়ে ‘কুমারী’ থাকলেও বাচ্চার জন্ম দিতে পারে। কিনা, অলৌকিক ক্ষমতা বলে কিছু আছে কিনা, শিগগিরই যিশুর আবার আসা সম্ভব কিনা এবং যুগাস্তে যিশুর পুনরভ্যুত্থান হওয়াও আদৌ সম্ভব কিনা—এ জাতীয় প্রশ্ন করার মানসিকতাই Fundamentalist-দের ছিল না! আর এদের মধ্যে একটি তো, অর্থাৎ যিশুর শিগগিরই মর্তে আবির্ভূত হয়ে মানবজাতিকে উদ্ধার করার বিশ্বাসটিতে, ইতিমধ্যে ভুলই প্রমাণিত হয়েছে; প্রায় দেড়শ’ বছর কেটে গেল, ‘তিনি’ আর এলেন না।
(৭) এটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক শ্রেণীবিভাজন ও বৈষম্য, নারী-পুরুষ দ্বন্দ্ব তথা পুরুষ আধিপত্য ইত্যাদিকে অস্বীকার করে। কৃত্রিম ধর্মই তার প্রধান বিবেচ্য। এ ক্ষেত্রে একই ধর্ম মতাবলম্বী বিভিন্ন ব্যক্তিদের সে পারস্পরিক সুহৃদ বলে ভাবতে শেখায়, যদিও তাদের মধ্যে বৈষম্য ও শাসক-শাসিতের বিভাজন রয়েছে। এই বৈষম্য ও বিভাজনকে দূর করা দূরে থাক, তাকে কমিয়ে তোলার আন্দোলনেরও সে বিরোধী। এরই একটি বহিঃপ্রকাশ ঘটে কট্টর কম্যুনিজমবিরোধিতার মধ্যে। সামরিক খাতে ব্যয় বাড়ানোর মত নানা পদক্ষেপ নিয়ে সে শাসকশ্রেণীর হাতকে শক্তও করতে চায়। সব মিলিয়ে ফান্ডামেন্টালিজম হচ্ছে শাসক শ্রেণীর স্বার্থবাহী, জনস্বার্থবিরোধী, পুরুষ আধিপত্যকামী একটি মতবাদ।
(৮) আমেরিকার Fundamentalist-দের আরেকটি দিকও গুরুত্বপূর্ণ যে, তারা তাদের কাজকর্ম বা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ভাবে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা বা রাষ্ট্রযন্ত্রের শীর্ষে বসার চেষ্টা করে নি। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ও রাষ্ট্রনীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা তারা অবশ্যই করেছে (প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় বাড়ানো বা কঠোর কম্যুনিষ্ট-বিরোধী বৈদেশিক নীতির জন্য আন্দোলন করার মত কাজকর্মের মধ্যে), কিন্তু তাদের নীতি ও বিশ্বাস অনুযায়ী নিজেরা নেতৃত্ব দখল করে সমগ্র রাষ্ট্রকে পরিচালিত করা, কিংবা খৃস্টান বা ফান্ডামেন্টলিস্ট রাষ্ট্র গড়ে তোলা—এমন আশা বা দাবী তারা করে নি, অন্তত তা ততটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে নি।
আমেরিকার ফান্ডামেন্টালিস্টদের এই সব বৈশিষ্ট্য–বিশেষত প্রথম সাতটি চারিত্রিক দিক যাদের মধ্যে দেখা যায়, তাদেরই সাধারণভাবে মৌলবাদী হিসেবে এবং এ ধরনের মানসিক ও তাত্ত্বিক প্রক্রিয়াকে মৌলবাদ হিসেবে অভিহিত করা যায়। সাংগঠনিকভাবে ব্যাপারটি মূলত ধর্মীয় পরিমণ্ডলে সীমিত থাকলেও, ব্যাপকতর অর্থে এই ধরনের মানসিকতাকেই মৌলবাদী মানসিকতা বলা যায়। সব সময় তা যে ধর্ম ও ঈশ্বর-বিশ্বাসের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে বা থাকছে, তার কোন মানে নেই। রাজনৈতিক মতাদর্শগত ক্ষেত্রেও এই মানসিকতার প্রসার ঘটতে পারে এবং তা ঘটেছেও। এমন কি মার্কসবাদ নামক যে দার্শনিক চিন্তা চূড়ান্ত অর্থে ধর্ম ও ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তাকে ও বাস্তব অস্তিত্বকে অস্বীকার করে এবং দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সব কিছু বিচার করার কথা বলে, ঐ মার্কসবাদকে সামনে খাড়া করে রেখেও এমন মৌলবাদী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। সহজভাবে বললে ব্যাপকতর অর্থে এইভাবে মৌলবাদকে দুটি মোটা দাগে ভাগ করা যায়-ধর্মীয় মৌলবাদ ও রাজনৈতিক মৌলবাদ।
এখনকার ধর্মীয় মৌলবাদ সম্পর্কে আরো কিছু কথা বলার আগে অন্যান্য কয়েকটি প্রাসঙ্গিক দিকেরও উল্লেখ করা দরকার। সম্প্রতি যাদের মৌলবাদী হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে (যেমন আন্তর্জাতিক খৃস্টীয় বা ইসলামী মৌলবাদীরা কিংবা ভারতের হিন্দু মৌলবাদীরা) তাদের ক্ষেত্রে আরো কয়েকটি বৈশিষ্ট্যও সৃষ্টি হয়েছে, যেমন–
(১) বর্তমানে এটি আরো জঙ্গী ও হিংস্র। আমেরিকার ঐ ফান্ডামেন্টালিস্টরা নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে দাঙ্গার জন্ম দিয়েছে, মানুষ খুন করেছে বা শত শত মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছে—এমনটি নয়। অবশ্য তাদের একেবারে নিরীহ ভাবারও কারণ। নেই, কারণ আমেরিকায় ম্যাকার্থিবাদের সৃষ্টিতে এবং বিপুল সংখ্যক কমিউনিষ্ট নিধনে তাদের পরোক্ষ ভূমিকা ও উৎসাহ ছিলই। তবু তা ঘটেছে তাদের সৃষ্টির পরবর্তী পর্যায়ে। শুরুর দিকে ধৰ্মরক্ষা ও ধর্মবিরোধী বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের বিরুদ্ধে আদর্শগত লড়াই ছিল প্রধান দিক। কিন্তু এখনকার হিন্দু-মুসলিম ইত্যাদি ধর্মীয় মৌলবাদীরা এই ধরনের মানসিকতার সঙ্গে গুণগতভাবে উচ্চতর ও লক্ষ্যণীয় মাত্রায় প্রত্যক্ষভাবে হিংস্রতাকেও সংযুক্ত করেছে। ১৯৭৮-এ ইরানে ইসলামী মৌলবাদীদের হাতে ৫৮ জন আমেরিকানের বন্দী থাকার উদাহরণ কিংবা আফগানিস্থানে রুশ সামরিক উপদেষ্টাদের হত্যার ঘটনা জানা আছে। এ-ও জানা আছে যে হিরোসিমা-নাগাসাকিতে যত মানুষ বোমার আঘাতে মারা গেছিলেন, তার চেয়ে বেশি মানুষ এই ভারতেই ধর্মকেন্দ্ৰিক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রাণ হারিয়েছেন; তারই ধারাবাহিকতায় ‘রামরথ’ বের করে দাঙ্গার উস্কানি দিতে এই মৌলবাদীরা এখনো কোন ইতস্তত করে না। পরিণতি জানা সত্ত্বেও অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ভাঙ্গ আর উসকানি দিতে তাদের হৃদয়ে এতটুকু ভালবাসা ও মনুষ্যত্ব জাগে না। (অযোধ্যার পরে আসছে মথুরা, বারাণসী ও আরো কয়েকশত ‘উসকানি’-অর্থাৎ হিন্দু মৌলবাদের অন্তহীন অমনুষ্যত্ব।) কোরাণকে অপমানের ছুতো তুলে মুক্তমনা ব্যক্তিদের হত্যা করতে বা হত্যার ফতোয়া দিতে, কিংবা তথাকথিত নৈতিকতার সামান্য বিচ্যুতিতে নৃশংস শাস্তি দিতে, এদের হাত এতটুকু কাঁপে না।
Fundamentalism-এর ঐতিহ্যে এই ভয়াবহ মাত্রায় হিংস্রতার সংযোজন সাম্প্রতিক মৌলবাদীদের একটি বিশেষ কৃতিত্ব।
এবং এক্ষেত্রে ফ্যাসিবাদের সঙ্গে তার যথেষ্ট মিল রয়েছে। (ফ্যাসিবাদ প্রথম দেখা দেয়। ১৯১১তে ইটালিতে এবং ফ্যাসিবাদের সন্ত্রাসবাদী একনায়কত্ব বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকে জার্মানিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফ্যাসিবাদকে ফাইন্যান্স পুঁজির সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল একনায়কতন্ত্র হিসেবে অভিহিত করা হয়। এদিক থেকে ধর্মীয় মৌলবাদের সঙ্গে তার কিছু তফাৎ হয়তো রয়েছে। কিন্তু কর্তৃত্ববাদী হিংস্ৰতা সহ নানা দিকে তাদের মিলও প্রচুর।)
(২) এখনকার মৌলবাদীদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল তথা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা ধর্মের মূল ভিত্তিকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টার চেয়ে অনেক বেশি তীব্র। এই ব্যক্তিগত বা শ্রেণীগত স্বার্থসিদ্ধির সংকীর্ণ মানসিকতা মৌলবাদী সংকীর্ণতাকে আরো মরিয়া, জঙ্গী ও অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলেছে। সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগের মৌলবাদী উত্তরাধিকারী জামাতে ইসলামী (যেমন তার বাংলাদেশী সংস্করণ) কিংবা আর এস এস-ভি এইচ বি-বিজেপি চক্র রাজনৈতিক দল হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করছে। এবং বিশেষ দেশে বা রাজ্যে তারা ক্ষমতা দখল করতে ইচ্ছক। ধৰ্মরক্ষার চেয়ে গদিতে বসার আকাঙ্খীই স্পষ্ট হচ্ছে, যদিও আগেও ধর্মরক্ষার নামে সিংহাসনে বসার উদাহরণ ছিলই। এখন সব ধর্মের মৌলবাদী সংস্থার মধ্যে এমন রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারটা সর্বজনীন না হলেও, Fundamentalism-এর র তকীকরণ সাম্প্রতিক মৌলবাদের অন্যতম একটি পার্শ্ববৈশিষ্ট্য।
তবে মৌলবাদের রাজনৈতিকীকরণ ও রাজনৈতিক মৌলবাদ—এ দু’টি ভিন্ন জিনিষ। মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের তথা মানসিকতার দিক থেকে তারা অভিন্ন কিন্তু মৌলবাদের রাজনৈতিকীকরণ আসলে ধর্মীয় মৌলবাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের সাম্প্রতিক আকাঙ্খারই বহিঃপ্রকাশ। আমেরিকার Fundamentalist-দের প্রধানতম কাজের ক্ষেত্র ছিল ধর্ম (এখানে খৃস্ট ধর্ম)। তার কিছু রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ হয়তো ছিল, কিন্তু তা ছিল গৌণ একটি দিক। কিন্তু ভারতীয় জনতা পাটি বা জামাতে ইসলামীদের কাজের ক্ষেত্র ধর্মের গণ্ডি ছাড়িয়ে আরো অনেক স্পষ্টভাবে ও সুনির্দিষ্টভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রসারিত; ধর্ম ও রাজনীতির মধ্যে পাল্লা বিচারে ধর্মের দিকে পাল্লা ভারী তো নয়ই, বরং উল্টোটাই,–অন্তত সমান তো বটেই। অন্যদিকে রাজনৈতিক মৌলবাদের ক্ষেত্রে ধর্মের ব্যাপারটি নগন্য এমনকি শূণ্যও হতে পারে, যেমন মার্কসীয় মৌলবাদীদের’ ক্ষেত্রে। ‘মৌলবাদের রাজনৈতিকীকরণ’ কথার মধ্যে আসলে ধর্মীয় মৌলবাদের রাজনৈতিকীকরণকেই বোঝানো হচ্ছে—ধর্মীয় মৌলবাদের ক্ষেত্রে যা আগে এমনভাবে ছিল না। অন্যদিকে ‘রাজনৈতিক মৌলবাদ’ বলতে রাজনৈতিক দলের মধ্যে মৌলবাদী কিছুমানসিকতার প্রতিফলনকে বোঝানো হচ্ছে মাত্র যা কাম্য নয়। বিশেষত যারা মার্কসবাদের মত দর্শনের কথা বলেন তাদের ক্ষেত্রে এবং সাধারণভাবে সমস্ত ধরনের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলের পরিপ্রেক্ষিতে।
তবে ‘মৌলবাদ’ কথাটি স্বাধীনভাবে এখনো শুধুমাত্র ধর্মীয় মৌলবাদকেই বোঝায়। যদি তার আগে অন্য কোন বিশেষণ বসানো হয় তবে তা কিছু ভিন্নতর তাৎপর্য বহন করতে পারে, যেমন সাম্প্রদায়িক মৌলবাদ, রাজনৈতিক মৌলবাদ। এমনকি মৌলবাদের আরো সাধারণীকরণ করে অর্থনৈতিক মৌলবাদ, যুক্তিবাদী মৌলবাদ ইত্যাদি কথাগুলিকেও ব্যবহার করা যায়, —যদি অর্থনীতি ও যুক্তিবাদের নাম করে একই রকম গোঁড়ামি, অসহিষ্ণুতা, সামাজিক ক্ষতিকর প্রভাব ইত্যাদি একই রকম ভাবে দেখা যায়।
আবার মৌলবাদ-মৌলবাদী কথাগুলি ব্যবহৃত হতে হতে অনেক সময় অনেকের দ্বারা শুধুমাত্র ‘গোঁড়ামি’ বোঝাতেই সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়। (যেমন, ‘শঙ্করাচার্যের ফতোয়ায় রবিবার কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে মহিলার বেদপাঠ নিষিদ্ধ হওয়ায় স্তম্ভিত বহু সংগঠন। তাদের সম্মিলিত মঞ্চ মানব সংহতি-র তরফে আজ ক্ষোভ জানিয়ে বলা হয়েছে, এই ফতোয় হিন্দু মৌলবাদেরই দম্ভ। বাংলার মানুষ তা মেনে নেবে না। …’ আজকাল, ১৮ই জানুয়ারী,১৯৯৪)
হিন্দু, ইসলাম, খৃষ্ট, শিখ ইত্যাদি নানা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মমতকে কেন্দ্র করে যখন মৌলবাদী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তখন তা ধর্মীয় মৌলবাদ। এই ধরনের প্রায় সব ধর্মই ঈশ্বর নামক এক অলীক ও মানুষেরই মনগড়া শক্তিতে বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। তাই স্বাভাবিক ভাবেই ধর্মীয় মৌলবাদীরা সবাই সাধারণভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাসী এটি বলাটা বাহুল্য মাত্র। তবে তাদের সবার ক্ষেত্রে এই বিশ্বাস আন্তরিক না-ও হতে পারে। যেমন ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দু বা মুসলিম মৌলবাদীদের সবাই পরম ঈশ্বরভক্তি কিনা তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এদের অনেকের ক্ষেত্রেই ঈশ্বর ও ধর্মকে সামনে দাঁড় করিয়ে অর্থাৎ সাধারণ ধর্মবিশ্বাসী মানুষদের ভুলিয়ে, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের ধান্দাটিই বড়। এ ধরনের তথাকথিত মৌলবাদীরা আসলে প্রকৃত মৌলবাদীর মর্যাদা পাওয়ারও যোগ্য নয়, তাদের আরো নিকৃষ্টতর কোন বিশেষণে ভূষিত করা যায় এবং উচিতও। একজন বিশুদ্ধ মৌলবাদী, তার সমস্ত সংকীর্ণতা ও প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র নিয়েও, ঐশ্বরিক শক্তিতে বিশ্বাসের ব্যাপারে অন্তত অটল। তার এই অনড় অটল বিশ্বাস বা ভক্তিই তাকে মৌলবাদী করেছে,–ঐশ্বরিক গ্রন্থের সামান্য অমর্যাদা সে সহ্য করে না। বা তার ভিত্তিটাকে নাড়াতে উপক্রম যে-ই করে (কোন মানুষ বা তত্ত্ব) তাকে সে নিজের কাছের বলে গ্রহণ করতে পারে না। তারই জন্য তার মধ্য থেকে উদারতা ও অন্যের প্রতি সহিষ্ণুতা বিনষ্ট হয়, এ কারণেই সে প্রয়োজনে নিজেকে ও নিজের সমাজকে দু’এক হাজার বছর পিছিয়ে নিয়ে যেতেও রাজী। হিন্দু মৌলবাদীরা বেদকে, মুসলিম মৌলবাদীরা কোরানকে, খৃষ্টান মৌলবাদীরা বাইবেলকে সনাতন অপৌরুষেয়, সমালোচনা ও পরিমার্জনার উর্ধে সর্বোচ্চ নেতৃত্ব-দায়ী একটি ভিন্ন সত্তা হিসেবে মনে করে। কিন্তু বেদ বা কোরানকে শ্রদ্ধার সঙ্গেও হুবহু না মেনে চলা এবং তাদের সম্পর্কে সামান্য কিছুও না জানা (স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় ‘চার পুরুষ ধরে এক খণ্ড বেদও না দেখা’) ধর্মীয় মৌলবাদীর অভাব নেই। ওরা আসলে মৌলবাদের পচা ডোবায় ভেসে থাকা পচা পাতার মত।
ধর্মীয় মৌলবাদীদের থেকে রাজনৈতিক মৌলবাদীদের একটি বড় তফাৎ এখানে যে, রাজনৈতিক মৌলবাদীরা ঈশ্বরে বিশ্বাসী নাও হতে পারে, এমনকি ঈশ্বরে অবিশ্বাসী বা তথাকথিত নাস্তিক (অন্তত বাহ্যিকভাবে) হতে পারে। ধর্মনিরপেক্ষ কোন রাজনৈতিক মতাদর্শ কিংবা মার্কসবাদের নাম করে, কিছু কিছু রাজনৈতিক দল বা তথাকথিত কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে এই লক্ষণ যখন দেখা যায়, তখন ধর্মীয় মৌলবাদীদের থেকে তাদের এই পার্থক্যের দিকটি পরিষ্কার হয়। কিন্তু সে ক্ষেত্রে তারাও ঈশ্বরের পরিবর্তে তাদের পিতৃসুলভ তত্ত্বটিকে একই ভঙ্গিমায় একই আসনে বসায়।
‘মাকর্সবাদ সর্বশক্তিমান, কারণ ইহা সত্য’–এই ধরনের পোস্টার ও প্রচার বাংলায় এখন বেশ দেখা যাচ্ছে। তথাকথিত মার্কসবাদী বা কম্যুনিষ্টদের মধ্যে অন্যত্রও এই মানসিকতার রকমফের দুর্লভ নয়। (যথাসম্ভব বিশ্বের নানা স্থানে মার্কসবাদ বা কম্যুনিজম ও সমাজতন্ত্রের তথাকথিত বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়ে আপন তত্ত্বের মাহাত্ম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার তাড়নায় তা করা হয়েছে।) মাকর্সবাদকে এইভাবে বিচ্ছিন্নভাবে ‘সর্বশক্তিমান’ হিসেবে ব্যাপক প্রচার করার বালখিল্যসুলভ (কিংবা অমার্কসীয়) প্রচেষ্টার মধ্যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরে ভক্তির দিকটিই ভিন্নভাবে পরিস্ফুট হয়। মার্কস নিজেও কখনো তাঁর নিজের ‘তত্ত্বকে’ সর্বশক্তিমান হিসাবে দাবী বা প্রচার করেছেন বলে জানা নেই। বরং যে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদী দর্শন তার ভিত্তি, ঐ অনুযায়ী মার্কসের তত্ত্বেরও যুগোপযোগী পরিবর্তন, বৈজ্ঞানিক পরিমার্জনা ও গোঁড়ামিযুক্ত সমালোচনা সুস্থ ও অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এই রাজনৈতিক মৌলবাদীরা (এক্ষেত্রে আরো সুনির্দিষ্টভাবে বললে মার্কসীয় মৌলবাদীরা) ধর্মীয় মৌলবাদীদের মত অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতেও বাধ্য। তাদের ঐ মৌলবাদী চরিত্রেরই একটি বহিঃপ্রকাশ মার্কসবাদকে সর্বশক্তিমান হিসেবে প্রচার করার মধ্যে। অথবা কোন ধরনের সমালোচনা পর্যালোচনা ও পরিমার্জনার মানসিকতা ও যোগ্যতা অর্জন না করে এবং সেগুলিকে মুক্ত মনে গ্ৰহণ না করার মানসিকতা নিয়ে, অন্ধভাবে নিজেদের আঁকড়ে রাখা তত্ত্বকে সর্বশক্তিমান হিসেবে গণ্য করার সঙ্গে সঙ্গে মৌলবাদী চরিত্রও তারা অর্জন করে ফেলে (একই ধরনের অন্ধবিশ্বাস, হিংস্রতা, পরমত অসহিষ্ণুতা, সংকীর্ণতা তথা অনুদার দৃষ্টিভঙ্গী, মূল রাজনৈতিক গ্রন্থটিকে সর্বোচ্চ ভাবা ইত্যাদি)। কিংবা উভয়ই। প্রকৃত বিচারে এই গোঁড়ামি মার্কসবাদ অনুসরণে নিজেদের অক্ষমতা ও ভন্ডামি এবং হয়তো বা তজনিত হতাশারই বহিঃপ্রকাশ।
বিজ্ঞানে চরম সত্য বলে কোন কিছু নেই। একটি বিশেষ সময়ে তখনকার জ্ঞান অনুযায়ী এবং তথ্য, যুক্তি, প্রমাণের সাহায্যে কোন তত্ত্বকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করা হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মন সর্বদাই তার বিকাশের জন্য আগ্রহী এবং পরবর্তীকালে নতুনতর তথ্য-প্রমাণের সাহায্যে পুরনো সত্য পাল্টে নতুন একটি সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্টা। (এমন কি আপেক্ষিকতার তত্ত্ব, কোয়ান্টাম তত্ত্ব ইত্যাদির আরো বিকাশে বিশুদ্ধ বস্তুবাদী দর্শনের বর্তমান রূপটিও পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।) উপযুক্ত তথ্য-যুক্তি ও প্রমাণের সাহায্যে নতুনতর সত্য প্রতিষ্ঠিত করা গেলে বিজ্ঞানীরা নিদ্বিধায় তাকে গ্ৰহণ করেন এবং পুরনো সত্য।’-কে মোহমুক্ত ভাবে বিসর্জন দেন। অন্ধবিশ্বাসী, গোঁড়া বা মৌলবাদীদের থেকে তাদের এখানেই বড় তফাৎ। তাই বেদ বাইবেল বা কোরানের শিক্ষাকে অপরিবর্তনীয় ও সমালোচনার উর্ধে বলে গণ্য করা যেমন ধর্মীয় মৌলবাদের বড় একটি লক্ষণ, তেমনই গান্ধীবাদ বা মার্কসবাদকে অপরিবর্তনীয় ও সমালোচনার উর্ধে বলে গণ্য করাটাও রাজনৈতিক মৌলবাদের লক্ষণ।
একইভাবে ‘সর্বশক্তিমান’ কথাটিও অবৈজ্ঞানিক ধারণার বহিঃপ্রকাশ। যে ধারণা ও কল্পনা থেকে ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান হিসেবে কিছু মানুষ শ্ৰদ্ধা ও ভয় করেছে, ঐ ধরনের ধারণা ও কল্পনা থেকেই কোন তত্ত্বকে একই ভাবে সর্বশক্তিমান বলার প্রবণতা জন্মায়। প্রকৃতি, পৃথিবী ও সমাজের সমস্ত সমস্যার সমাধান মার্কসবাদ বা এই জাতীয় একটি তত্ত্ব করে ফেলতে সক্ষম, এটি ভাবতে ভাল লাগলেও লগতে পারে, কিন্তু বাস্তবতা থেকে তা বহু দূরে। বড়জোর বলা যেতে পারে এই সব সমস্যার সমাধানে এ ধরনের একটি তত্ত্ব বর্তমান জ্ঞানে ও পরিবেশে সব চেয়ে বেশি কার্যকরী হিসেবে প্রচেষ্টা চালাতে সক্ষম। ভবিষ্যতে আরও কার্যকরী, আরো বিজ্ঞানসম্মত কোন তত্ত্ব মানুষ জানতেই পারে। কিন্তু এখনই একটিকে সর্বশক্তিমান হিসেবে ঘোষণা করার মধ্যে ভবিষ্যতের ঐ সত্যকে আন্তরিকভাবে গ্ৰহণ করার মানসিকতাটিকে নষ্ট করা হয়, মনকে ঐ ভাবে সত্যিকারে প্রস্তুত করাও যায় না।
‘মার্কসীয় মতবাদ সর্বশক্তিমান, কারণ ইহা সত্য’-এ কথাটি লেনিনের। (‘The Marxian doctrine is omnipotent because it is true’-Three sources and three component parts of Marxism, V.I. Lenin) যেহেতু লেনিন বলেছেন, অতএব কথাটি প্রচারযোগ্য, এই বিচারের চেয়ে লেনিন কেন বলেছেন এবং তার পেছনে যুক্তি কতটা রয়েছে,–এ ধরনের বিচার করাই যুক্তিযুক্ত। আর সত্যি কথা বলতে কি, বিচ্ছিন্নভাবে শুধু এই কথাগুলিকে বড় বড় করে তুলে ধরলে ভুল বোঝার সম্ভাবনাই বেশি। কোন বিশেষ তত্ত্ব বা মতবাদ সম্পর্কে এমন সাটিফিকেট প্রচার করার চেয়ে, বাস্তব কাজ ও আচার আচরণের মধ্যে ঐ তত্ত্ব বা মতবাদের যাথার্থ্য ও যৌক্তিকতা প্ৰমাণ করাটাই কাম্য ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। কাজে তা না করে, নিজেদের গোষ্ঠীভুক্ত ব্যক্তিদের ঐ তত্ত্বে প্রকৃত শিক্ষিত করার চেয়ে অন্য সংকীর্ণ ধান্দায় নিয়োজিত করাকে বেশি গুরুত্ব দিযে, এমন কি যারা এ কথাগুলি প্রচার করছেন তারা আদৌ ঐ তত্ত্বকে আত্মস্থ করে সৎভাবে কাজ করেন কিনা—এই বিতর্কের সৃষ্টি যেখানে হয়েছে—সেখানে তাদের এই আচমকা প্রচার একটি ভান ও প্রতারণা বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে।
লেনিন ঐ একই লেখায় আরো মন্তব্য করেছেন, ‘মার্কসবাদে ‘গোঁড়ামি’ জাতীয় কোন কিছু নেই…’ (‘There is nothing resembling ‘sectarianism’ is Marxism, in the sense of its being hide bound, petrified doctrine, a doctrine which arose away from the highroad of development of world civilisation.’) ভাববাদী দর্শনের বিপরীতে এবং অবশ্যই মৌলবাদী চিন্তাভাবনার বিপরীতে স্পষ্টভাবে যে তত্ত্ব গোঁড়ামি বর্জন করার কথা বলে, সেই তত্ত্বের প্রতিই গোঁড়ামি থাকাটা সেই তত্ত্বেরই বিরোধী। মাকর্সবাদের–বা যথার্থভাবে বল্পে বলা উচিত মার্কসীয় দর্শনের, যথার্থ্য এখানেই যে, সে নিজের প্রতি সহ সর্বত্র এই গোঁড়ামি থেকে মুক্ত হওয়ার কথা বলে এবং এও বলে যে, প্রকৃতিতে সব কিছুই পরিবর্তনশীল, কোন কিছুই স্থির নয় ইত্যাদি। এখনো অব্দি জানা বিভিন্ন দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসীয় দর্শনকে তার বিপুল বিস্তারী দিক নিয়ে, এ কারণেই যথার্থ ও বিজ্ঞানসম্মত হিসেবে গ্রহণ করা হয়।
কিছু সত্য আছে যা চরম সত্য (absolute truth)। যেমন ত্রিভুজের তিনকোণের সমষ্টি ১৮০ ডিগ্রি ইত্যাদি জাতীয় জ্যামিতিক সত্য কিংবা কাউকে দেখিয়ে যদি বলা যায় তার ঠাকুর্দা-ঠাকুমা বা বাবার মা ছিলেন। তবে তা চরম সত্যই। লেনিনও তার Materialism and Empirico-Criticism গ্রন্থে চরম সত্যের উদাহরণে বলেছেন, ‘না খেয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না’ এবং ‘শুধুমাত্র প্লেটোনিক প্রেমের সাহায্যে বাচ্চার জন্ম হবে না’, এগুলি চরম সত্য। কোন প্রমাণিত ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কেও তা একইভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু এই ধরনের উদাহরণই চরম সত্য কিনা তা নিয়েও বিতর্ক উঠতে উঠতে পারে। যেমন কেউ যদি না খায়, তবে তাকে ইনজেকশন করে পুষ্টির যোগান দিয়ে বঁচিয়ে রাখা যায়। তাই—’পুষ্টি ছাড়া মানুষ বেশিদিন ধাঁচে না’। এটি হয়তো চরম সত্য। (কিন্তু এতেও ফাঁকি খুঁজে পাওয়া সম্ভব।) আবার বর্তমানে যখন কৃত্রিম প্ৰজনন ও টেস্ট টিউব বেবি ইত্যাদির বিপুল অগ্ৰগতি ঘটছে, যেখানে দু একশ’ বছর পরে নারী পুরুষ প্লেটেনিক প্রেম করে গেলেও মানব সমাজে শিশুর জন্ম হবে না তা নিশ্চিত করে বলা মুস্কিল। তা অসম্ভব নয় বলেই মনে হয়। সেক্ষেত্রে লেনিনের কথাটি ভুল বলে প্রতিষ্ঠিত হবে। যেহেতু লেনিন বলেছিলেন ‘প্লেটোনিক প্ৰেম করে গেলে বাচ্চার জন্ম হবে না-এ মন্তব্যটি একটি চরম সত্য’, তাই ভবিষ্যতের ঐ রকম সম্ভাবনাকেও নস্যাৎ করাটা মৌলবাদী চিন্তার একটি প্রকাশ হিসেবেই বলা যায়। লেনিনের সময় কৃত্রিম প্রজনন সম্পর্কিত মানুষের জ্ঞান বর্তমান অবস্থার মত আদৌ ছিল না। তাই লেনিন উদাহরণ দিয়ে গিয়ে এমন কথা বলেছিলেন। তখনকার পরিবেশ ও জ্ঞানের স্তরে সেটাই সত্য ছিল। কিন্তু তাঁর মন্তব্যই চরম সত্য তা নয়। একইভাবে ভবিষ্যতে এমন কৃত্রিম প্রজননে জাত কোন প্রাণী বা মানুষের প্রচলিত অর্থে সুনির্দিষ্ট বাবা-মা, ঠাকুমাঠাকুর্দা না-ও থাকতে পারেন। সেক্ষেত্রেও পূর্বোক্ত মন্তব্যটি পরম সত্য নয় বলে প্রমাণিত হয়। পরবর্তীকালে নতুন জ্ঞান পুরনো সত্যকে এইভাবেই বাতিল করে বা পরিমার্জিত করে। মৌলবাদী মানসিকতা এই পরিবর্তন ও পরিমার্জনাকে গ্ৰহণ করতে চায় না, যেমন চায়নি আমেরিকার ‘Fundamentalist’-র বাইবেলের ক্ষেত্রে বা মুসলিম মৌলবাদীরা চায় না কোরানের প্রসঙ্গে কিংবা হিন্দুরা বেদ উপনিষদ জাতীয় ধর্মগ্রন্থ প্রসঙ্গে।
‘সত্য’ (Truth) সম্পর্কে পূর্বোক্ত কিছু চরম সত্য (যাও হয়তো আপাত) ছাড়া, সাধারণভাবে কোন কিছুকে এইভাবে চিহ্নিত করা অবৈজ্ঞানিক। মরিস কনফোর্থ মন্তব্য করেছেন, ‘সাধারণভাবে, বিজ্ঞান চরম সত্যে আদৌ আগ্রহী নয়। প্রকৃতপক্ষে একবার যদি কোন সিদ্ধান্তকে চরম সত্য হিসেবে বলে দেওয়া হয়, তাহলে পরবর্তী অনুসন্ধানের সমস্ত দরজাই বন্ধ করে দেওয়া হয় : চরম সত্যই যদি জানা হয়ে যায়, তবে তো আরো গবেষনার কোন প্রয়োজনই থাকে না, চরম সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার বা জেনে নেওয়ার দাবী তাই প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান-বিরোধী, কারণ এমন দাবী আমাদের আরো গবেষণা চালাতে, আমাদের জ্ঞানের বিকাশ ঘটাতে, সত্যের কম কাছাকাছি অবস্থা থেকে বেশি কাছাকাছি অবস্থায় পৌঁছতে, অন্য কথায় বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমাদের বাধা দেয়’।
বিচ্ছিন্নভাবে মার্কসবাদকে ‘ইহা সত্য’ বলার মধ্যে ঐ চরম সত্য জেনে ফেলার দাবীই যেন বোঝায়। মার্কসবাদের সত্যতা ও চমৎকারিত্ব এইখানেই যে, কোন কিছুই যে ঐভাবে সত্য নয়, এটি উপলব্ধি করতে তা আমাদের শেখায় এবং এই কোন কিছুর মধ্যে সে নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করতেও দ্বিধা করে না। অ্যান্টি ডুরিং-এ এঙ্গেলস যেমন বলেছেন, ‘প্রকৃত পক্ষে ‘ভুল’ ও ‘ঠিক এই কথাগুলির মত গোঁড়া ও নীতিগত ভাবপ্রকাশকে বৈজ্ঞানিক কাজ নিয়ম করেই এড়িয়ে চলে, যদিও এই ধরনের কথার সঙ্গে কাজেকর্মে আমরা সর্বত্রই পরিচিত হই.এদের মাধ্যমে একটি সর্বোচ্চ চিন্তার সর্বোচ্চ ফলাফলকে আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলে; যে চেষ্টায় এক একটি উক্তির ব্যবসা করার শূন্যগর্ভ প্রবণতা থাকে।’ (‘Really scientific works therefore as a rule avoid such dogmatic and moral expressions as error and truth, while these expressions meet us everywhere in works…in which empty phrase mongering attempts to impose on us as the sovereign result of sovereign thought.’) সুবিধাজনক ভাবে এইভাবে এক একটি উক্তি বা ফ্রেজ (phase) তুলে নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে তার ‘প্রচার করার প্রবণতা না থাকলেই ভাল।
সত্য সম্পর্কে এ ধরনের বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীর পাশাপাশি এটিও বারংবার মনে রাখা দরকার এবং আবারো বলা দরকার যে, মার্কসবাদের মত কোন তত্ত্বই হোক বা পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে জাতীয় কোন বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণই হোক বা বিবর্তনবাদের মত কোন যুক্তিনির্ভর সিদ্ধান্তই হোক, যেটি সাম্প্রতিক জ্ঞান ও তথ্যের পরিপূর্ণ প্রয়োগ ঘটিয়ে সৃষ্টি হয়েছে সেগুলিকে তখনকার মত সত্য বলে গ্রহণ না করাটাও গোঁড়ামি, যা মৌলবাদী মানসিকতার সঙ্গে যুক্ত এবং যা মৌলবাদী ক্রিয়াকান্ডের জনক। সেগুলিকে ‘আরো সংশোধন করতে হবে, তাদের উন্নতি ঘটাতে হবে, নতুন অভিজ্ঞতা ও নতুন জ্ঞানের আলোয় তাদের নতুন করে ব্যাখ্যা করতে হবে। কিন্তু এই কারণেই সেগুলি অসত্য নয় : সেগুলি আংশিক ও তুলনামূলকভাবে সত্যের কাছাকাছি।’ (‘They require to be corrected, improved upon, restated in the light of new experience and new knowledge. But they are not for that reason untrue : they are partial, relative, approximate truth.’–Dialectical Materialism, Maurice Cornforth) ব্যাপারটি মার্কসবাদ সম্পর্কেও সত্যি। রাজনৈতিক অন্ধবিশ্বাস ও অসূয়া থেকে মুক্ত হয়ে ব্যাপারটি উপলব্ধি করলে, লেনিনের একটি বাক্যকে আক্ষরিক অর্থে ও বিচ্ছিন্নভাবে প্রচার করার প্রয়োজনীয়তা কমে আসে।
মার্কসীয় দর্শন প্রসঙ্গে একটু বেশি আলোচনা করা হলেও, প্রকৃতপক্ষে আরও একটু স্থূলভাবে তুলনা করলে, এই ধরনের সমস্ত দলীয় রাজনৈতিক মৌলবাদীদের মানসিকতা-আচার-আচরণের মধ্যে ধর্মীয় মৌলবাদের সাধারণ লক্ষণগুলিও দেখা যায়—(১) তারা ধর্ম-এর স্থানে নিজের দলীয় রাজনীতিকে বসায়, (২) ধর্মগ্রন্থের জায়গায় বসায় রাজনৈতিক দলিলপত্ৰকে, (৩) নিজের দলীয় রাজনীতিকে যা বিরোধিতা করে বা সমালোচনা করে, তাকে খোলামনে রাজনৈতিক বিতর্কে না। নিয়ে গিয়ে উগ্র ও হিংস্রভাবে বিরোধিতা করে, (৪) রাজনৈতিক উদারতা ও বিরোধী বা ভিন্ন রাজনৈতিক কর্মর প্রতি নৃত্যুনতম সন্ত্ৰমবোধ হারিয়ে ফেলে, (৫) দলীয় রাজনীতির প্রতি শৃঙ্খলা ও কেন্দ্রিকতার নামে একসময় দল ও নেতৃত্বের প্রতি প্রশ্নহীন বিশ্বাস ও দ্বিধাহীন আনুগত্য প্রকাশ করতে থাকে; দলে বা গোষ্ঠীতে যেই কেউ কিছু প্রশ্ন তোলে বা সমালোচনা করে তাকেই শত্রু বা শ্রেণীশত্ৰু, প্রতিক্রিয়াশীল, চক্রান্তকারী, পার্টিবিরোধী ইত্যাদি নানাভাবে চিহ্নিত করা হয়; অন্তত তার সঙ্গে সহজ সম্পর্ক আর থাকে না। মৌলবাদী সংগঠনের মত এই রাজনৈতিক নেতৃত্বও কর্মীদের কাছ থেকে চূড়ান্ত আনুগত্য প্রত্যাশা করে (৬) দলীয় রাজনীতির স্বার্থে হিংস্র আচরণ, খুন-জখম, দৈহিক-মানসিক-সামাজিক অত্যাচার চালানো ইত্যাদি তত্ত্ব লিপ্ত হয়। (৭) রাজনৈতিক ক্ষমতা তো লাভ করতেই চায়। তবে অবশ্যই সামাজিক সংস্কারমূলক কিছু ভূমিকা তার থাকে, ধর্মীয় মৌলবাদীদের থেকে এক্ষেত্রে তাদের কিছুটা পার্থক্য থাকতে পারে কিংবা নাও থাকতে পারে।
এ ব্যাপারে অবশ্যই কোন সন্দেহ নেই যে, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন বা বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতবাদ অনুযায়ী কাজ করেন, তাদের একটি অংশ যে অন্তত একটি স্তর অব্দি উদার ও মানবিক তাতে কোন সন্দেহ নেই। পরমত সহিষ্ণুতা, সমালোচনাকে গুরুত্ব দেওয়া, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বা ভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের সঙ্গে যৌথ কাজকর্ম করা, মত ও পথের পার্থক্য থাকলেও সুস্থ বিতর্কের মধ্য দিয়ে সামাজিক উন্নয়নের জন্য চেষ্টা চালানো ও পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তোলা-এগুলি বিরল কোন ঘটনা নয়।
ধর্মের প্রসঙ্গে ধর্মনিষ্ঠ বা ধামিক ব্যক্তির সঙ্গে ধর্মীয় মৌলবাদীদেরও এইভাবে একটি বড় তফাৎ রয়েছে। ধর্মনিষ্ঠ বা ধামিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে, নিজের ধর্মীয় বিশ্বাসকে, সেটি ঠিক ভুল যাই হোক না কেন, সৎভাবে অনুসরণ করাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান। নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি তা করেন। তার মধ্যে প্রশ্নহীন দ্বিধাহীন আনুগত্য ও বিশ্বাসের ব্যাপারগুলিও থাকে, কিন্তু মৌলবাদের অন্যান্য যে কয়েকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছিল সেগুলি অনুপস্থিত। তাঁর মধ্যে পরমতসহিষ্ণুতা, উদারতা ইত্যাদি অপ্রত্যাশিত নয়। অন্য ধর্মের বা গোষ্ঠীর মানুষের প্রতি ঘূণা বর্ষণ করা ও বিষোদগার করার ব্যাপারটি তাঁর মনেও আসে না। সবচেয়ে বড় কথা তার মধ্যে সংকীর্ণভাবে শুধু নিজ ধর্মের মানুষের নয়, সবার মঙ্গলের সামগ্রিক ইচ্ছাটাই বড় হয়ে দেখা দেয়। গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর, যিশু খৃস্ট থেকে গুরু নানক, শ্ৰীচৈতন্য, রামকৃষ্ণ-ইতিহাসের পাতায় এমন অনেক ধর্মনিষ্ঠ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। এদের মৌলবাদী বা সাম্প্রদায়িক বলার মত অবস্থা নেই, যদিও ধর্ম তাঁদের জীবন ও কাজের সবচেয়ে বড় জায়গা জুড়ে থাকে।
একইভাবে রাজনৈতিক মৌলবাদীদের সঙ্গে সৎ রাজনৈতিক কামীদের পার্থক্য রয়েছে। একদা একনিষ্ঠ গান্ধীবাদী বা কম্যুনিষ্ট কর্মীদের কথা আমরা জানি। মানুষ ধ ও তার সমাজকে ভালবেসে, নিজেদের রাজনৈতিক মতাদর্শকে সামনে রেখে, তার ত্রুটি বা সীমাবদ্ধত হয়তো থাকলেও, নিজের সংকীর্ণ স্বার্থের কথা মাথায় না। রেখে তারা কাজ করে গেছেন। এই ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ ছিল না বলেই, তাদের মধ্যে উদারতা ও মুক্তমনের পরিচয় পাওয়া যেত। প্রয়োজনে ভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীদের সঙ্গে যৌথ কাজ করা, তাদেরও বন্ধু ও সহযোদ্ধা হিসেবে গ্রহণ করার মহত্ত্ব বিরল কোন ঘটনা ছিল না। ভিন্ন রাজনৈতিক দলের কমী মানেই সে শত্রুস্থানীয়, তাকে প্রয়োজনে হত্যাও করা দরকার এবং কোনভাবেই তাকে ভালবাসা যায় না–এমন সংকীর্ণ মৌলবাদী মানসিকতা ছিল অনুপস্থিত। ধাৰ্মিক বা ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির মত এমন রাজনৈতিক কামী এখনো নিশ্চয়ই আছেন, কিন্তু পুরষ্কার রাজনৈতিক গোষ্ঠীতন্ত্র, তীব্র মেরুকরণ ও অনুদার মৌলবাদী মানসিকতার এর অর্থ এ অবশ্যই নয় যে, মৌলবাদী বলে প্রমাণিত কোন গোষ্ঠীর সঙ্গেও ঐক্য স্থাপন করা অমৌলবাদী মানসিকতার লক্ষণ। বরং উল্টোটাই। মৌলবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলে নিজেকেও কিছুটা মৌলবাদী হতে হয়। না হলে ঐভাবে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার মানসিকতটাই সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়। এ ধরনের রাজনৈতিক গাঁটছড়ার সঙ্গে প্রকৃত পক্ষে আদর্শের চেয়ে রাজনৈতিক সুবিধাবাদ, সংকীর্ণ গোষ্ঠী স্বাৰ্থ ব্যক্তিগত নোংরামির ব্যাপারটিই বেশি।
তাই দেখা যায় রাজনৈতিক মৌলবাদীরা মার্কসবাদ বা গান্ধীবাদকে সামনে রেখেও মুসলিম লীগ বা বিজেপি-র মত সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে সরকার গড়া থেকে পঞ্চায়েত বানানো পর্যন্ত নানা স্তরে ক্ষমতা লাভ করার চেষ্টা করে। ভারতের তথাকথিত মার্ক্সবাদীরা মুসলিম লীগের সঙ্গে কেরলে একদা সরকার গঠন করেছে। হিন্দু মৌলবাদীদের সঙ্গে যুক্ত হয়েও কংগ্রেসকে সরিয়ে জাতীয় ফ্রন্টের বিশ্বনাথপ্রতাপ সিং-কে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছে; তখন যুক্তি দেখিয়েছিল কংগ্রেসের পরিবারতন্ত্রকে উচ্ছেদ করা ছিল সব চেয়ে বড় কাজ। কিন্তু এসবে প্রকৃত লাভ হয়েছে হিন্দুমৌলবাদী রাজনৈতিক দলটির। লোকসভায় প্রতিনিধি সৎখ্যা তারা এক অঙ্কের থেকে তিন অঙ্কে নিয়ে যেতে পেরেছে। ধর্মীয় মৌলবাদীদের এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠায় বড় ভূমিকা নিয়েছিল তথাকথিত কম্যুনিষ্টরা।
বাংলাদেশেও কমিউনিষ্ট পার্টি অব বাংলাদেশ (সি পি বি) জামাতে ইসলামীর মত মুসলিম মৌলবাদীদের সঙ্গে আটের দশকের শেষদিকে ‘ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে লিপ্ত হয়েছিল। তখনো তারা কৌশল হিসেবে সামরিক শাসনকে উচ্ছেদ করাকে প্রধান কাজ হিসেবে মনে করেছে। তখন (১৯৮৭) বদরুদিন উমর মন্তব্য করেছিলেন, ‘আওয়ামী লীগ, বি এন পি, বাকশাল, সিপি বি এবং বামপন্থী নামধারী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ‘গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মাধ্যমে জামাতে ইসলামী এখন আওয়ামী লীগ ও সিপিবি মার্ক লোকেদের কাছেও রাজনৈতিক, মিত্র হিসাবে বেশ ভালভাবেই গ্রহণযোগ্য হয়েছে। জামাতে ইসলামের পক্ষে এই কীর্তি অর্জন করা উপরে উল্লিখিত তথাকথিত গণতান্ত্রিক, বামপন্থী ও কমিউনিষ্ট নামধারী সংগঠনগুলির নিদারুণ অবক্ষয় ও চরিত্রহীনতার ফলেই যে অনেকাংশে সম্ভব হয়েছে একথা বলাই বাহুল্য।’ ভারতের ক্ষেত্রে জামাতে ইসলামীর পরিবর্তে ভারতীয় জনতাপাটিকে (ও তার ধর্মভাইদের) বসালে, ঐ একই মন্তব্য এদেশের ‘তথাকথিত গণতান্ত্রিক, বামপন্থী ও কমিউনিষ্ট নামধারী সংগঠনগুলির’ জন্য ব্যবহার না করার কোন কারণ নেই। শ্রদ্ধেয় বিমলকৃষ্ণ মতিলাল এই কারণেই মন্তব্য করেছেন, ‘উদারনৈতিক নেতারা যখন ক্ষমতার লোভে মিথ্যার ব্যবসা আরম্ভ করেন-মৌলবাদের অভ্যুত্থানকে তখন আর রোধ করা যায় না।’ (মৌলবাদ কি ও কেন?)
পারিবারিক শাসন ও সামরিক শাসনকে উচ্ছেদ করার কর্মসূচীকে খারাপ কিছু ভাবার কারণ নেই। কিন্তু তার জন্য সুস্থতর কোন উপায় না গ্ৰহণ করে ধর্মীয় মৌলবাদীদের হাত শক্ত করা ও তাদের উত্থানে সাহায্য করার ভয়াবহ ঢেঁকীশালের মধ্যে শুধু অবক্ষয়, চরিত্রহীনতা, দেউলিয়াপনা ও সৃজনশীলতার অভাব নয়, মৌলবাদের প্রতি তাদের প্রচ্ছন্ন সহানুভূতির ব্যাপারেও সন্দেহ জাগে। আর বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক সহ অনেক নেতারাই তো নিজেদের নির্বাচনী ইস্তাহারে (১৯৯১) আল্লা হো আকবর’ যুক্ত করেছিলেন; এও জানা আছে যে পার্টির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক মহম্মদ ফরহাদ-এর মত কম্যুনিষ্ট নেতার মৃত্যুতে পার্টি অফিসে মিলাদ-এর মত ধর্মীয় অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল। এদেশের একম্যুনিষ্টরাও জনসংযোগের নাম করে পাড়ার দুর্গাপূজা থেকে শুরু করে যমপূজার মত নানা ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানে মদত দেন, ভোটের স্বার্থে জাত পাতের রাজনীতি করতে পিছপা হন না, সংরক্ষণের নাম করে জাত-পাতের বিভাজনকে শক্তিশালী করেন। আর ‘কম্যুনিষ্ট’ সদস্যরাও পূজা-শ্ৰাদ্ধ-বৈদিক মন্ত্র পড়ে বিয়ে করা জাতীয় নানা ধরনের ধর্মীয় অনাচার করেন হাজারো গালভরা যুক্তি দেখিয়ে। এদেশের একদা কত কম্যুনিষ্ট কর্মর মার্কসবাদের প্রতি নিষ্ঠ, ত্যাগ, সংগ্রাম ও রক্তক্ষরণের স্মৃতিকে পায়ে মাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। অধুনা এই সব মার্কসীয় দর্শনে অশিক্ষিত ও এই ধরনের ক্ষমতালোভী, স্বার্থপর কমীবৃন্দ ও নেতৃবৃন্দের বেশিরভাগই। তাঁদের চরিত্র বদলের সঙ্গেই যুক্ত ধর্মীয় মৌলবাদের উত্থানে সাহায্য করার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা। এঁরা ধর্মীয় মৌলবাদের প্রচ্ছন্ন সুহৃদ, রাজনৈতিক মৌলবাদী। আপাত ধৰ্মবিরোধী ব্যক্তিদের মধ্যেও নিজের বন্ধু খুঁজে নেওয়ার ও এইভাবে নিজেকে সঙ্গোপনে লুকিয়ে রাখার ক্ষমতা ধর্মীয় মৌলবাদের একটি বৈশিষ্ট্য। আর এই বৈশিষ্ট্য যার আছে সে যে অন্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে তার আরো বেশি সংখ্যায় কাছের লোক পাবে তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। জন্মসূত্রে হিন্দু কিন্তু কোনভাবে কম্যুনিষ্ট পার্টির সঙ্গে যুক্ত, এমন মানুষদের মধ্যেও বেশ কিছু জন আছে যারা হিন্দু মৌলবাদী সংগঠনগুলির মতই মনে মনে, মনে করে যে, মুসলিমদের একটু কড়কে দেওয়া দরকার, বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে বেশ আচ্ছা শিক্ষাই দেওয়া গেছে ইত্যাদি। আর কংগ্রেসের মত অন্যান্য দলগুলিতে তো কথাই নেই। ভোটের সময় বিজেপি যাদের ভোট পায় তাদের একটা অংশই একসময় কংগ্রেসকে ভোট দিত বা কংগ্রেসের সমর্থক ছিল। তাই ত্রিপাক্ষিক ভোটযুদ্ধে কংগ্রেস-বিজেপি বাদে তৃতীয়পক্ষের লাভ হয়ে যায় বেশি।
ব্যাপারটি খুব একটা অস্বাভাবিক নয়, যখন এটি অজানা নয় যে কংগ্রেসের তথাকথিত স্বাধীনতা আন্দোলন, মুখে যাই হোক না কেন, কার্যত দাঁড়িয়েছিল হিন্দুদের (বর্ণহিন্দুদের!!) স্বাৰ্থবাহী আন্দোলন। স্বদেশী যখন জন্মসূত্রে হিন্দু তখন তার কাছে এই হিন্দুত্বই বড় এবং মুসলমানকে, এমনকি সহযোদ্ধা মুসলিমকেও, অস্পৃশ্য বলে। ঘূণা করেছে। এরই একটি বাস্তব চিত্র বর্ণনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ-’হিন্দু মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে, কিছুকাল পূর্বে স্বদেশী অভিযানের দিনে একজন স্বদেশী প্রচারক এক গ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই।’ (লোকহিত)
স্পষ্টতঃ এইসব কর্মীদের অন্য যা শেখানো হোক না কেন, ধর্মমোহমুক্ত হবার শিক্ষাটিকে অন্যতম প্রাথমিক প্রয়োজন হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। ফলত যা হওয়ার হয়েছে, —তথাকথিত স্বাধীনতার আগেও যেমন, পরেও তেমনি, ধর্ম সুযোগ পেলেই মৌলবাদে পরিণত হওয়ার নিজস্ব প্রবণতা নিয়ে ভারতের এই বৃহত্তম রাজনৈতিক দলটির মধ্যে নিজেকে পরিপুষ্ট করেছে।
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে কর্মীদের ধর্মমোহমুক্ত করা সম্ভবও ছিল না,–বড়জোর কিছু ধর্মীয় সংস্কারের কথা বলা ছাড়া। এর জন্য বেশি গবেষণা করার প্রয়োজন নেই। জাতির জনক হিসেবে প্রচারিত যে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে ছাড়া এই কংগ্রেসকে ভাবা যায় না, তিনি তার অন্যান্য ইতিবাচক ও ঐতিহাসিক বহু দিক সত্ত্বেও প্রথমেই ছিলেন ঈশ্বরভক্তি ধর্মপ্ৰাণ ব্যক্তি এবং হিন্দু। ভারতের স্বাধীনতা বা ‘স্বরাজ’ আনার ব্যাপারে তার মূল বক্তব্যই ছিল, ‘সংগ্রামের মাধ্যমে নয়, ভগবানের আশীৰ্বাদরূপেই এই স্বরাজ স্বৰ্গ থেকে ভারতের উপর নেমে আসবে।’(ইন্ডিয়ান হোমরুল, ১৯২১) এমনকি নোয়াখালির দাঙ্গাবিধ্বস্ত পরিবেশে দাঁড়িয়েও তিনি হিন্দুদের ঈশ্বরবিশ্বাস ও রামনামে আস্থা রাখতে উপদেশ দিয়েছেন।–
‘ঈশ্বরে যদি আপনাদের অকপট বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে আপনাদের স্ত্রীকন্যার উপর, কেহই অমর্যাদাজনক আচরণ করিতে সাহসী হইবে না। আপনারা আপনাদের মুসলমান ভীতি ত্যাগ করুন; রামনামে যদি আপনাদের আস্থা থাকে তাহা হইলে আপনারা কখনোই পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া যাইবেন না।’ (নোয়াখালি ডাইরি) এই ‘রাম’ হিন্দুমৌলবাদীদেরও আদর্শ চরিত্র।
কুসংস্কারমুক্ত হয়ে, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে লড়াই চালানোর কথা বল্লেও যেন আমেরিকার ফান্ডামেন্টালিস্টদের মত, হিন্দুধর্মের আদি গ্রন্থগুলির প্রতি ছিল ভগবদভক্ত গান্ধীর গভীর শ্রদ্ধা।–
‘হিন্দুধর্মের দুইটি দিক আছে, একদিকে ঐতিহাসিক হিন্দুধর্ম—তাহার অস্পৃশ্যতা, কুসংস্কার, প্রস্তুরাদির পূজা ও পশুবলি প্রভৃতি; আর অপরদিকে গীতা, উপনিষদ এবং পতঞ্জলি যোগসূত্রের হিন্দুধর্ম-সেখানে অহিংসার চরম স্মৃর্তি, সর্বভূতের ঐক্য এবং সর্বব্যাপী, নিরাকার, অবিনশ্বর, অদ্বিতীয় ভগবানের পূজা। আমার কাছে অহিংসাই হইল হিন্দুধর্মের সর্বোত্তম মহিমা।’ (ঐ) আবার এই উদারনৈতিকতা ও সর্বধর্মের মানুষের (সর্বভূতের) ঐক্যের মানসিকতার মত নানা দিকের কারণে তাঁকে মৌলবাদী কখনই বলা চলে না, যদিও আবার তাদেরই মত তিনিও ছিলেন। কম্যুনিজম বিরোধী এবং কম্যুনিস্টদের সাহায্য করার জন্য ভগবানের কাছে আবেদনও জানিয়েছেন—
“পুজিপতিদের বিরুদ্ধে আমার কোন অনিষ্ট করার মনোভাব নেই। তাঁদের কোন ক্ষতি করার কথা ভাবতে পারি না। …ভগবান আপনাদের (কম্যুনিষ্টদের) বুদ্ধি ও যোগ্যতা দিয়েছেন। সেগুলিকে উপযুক্ত কাজে আপনার প্রয়োগ করুন। আপনাদের কাছে আমার নিবেদন এই যে, আপনারা আপনাদের বুদ্ধির দ্বার রুদ্ধ করবেন না। ভগবান আপনাদের সাহায্য করুন।’ (ইয়ং ইন্ডিয়া; ২৬শে মার্চ, ১৯৩১)
হিটলার থেকে হিন্দু-মুসলিম মৌলবাদীরা নারীদের প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করে হুবহু প্রায়ই একই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল গান্ধীরও —
‘জীবিকা অর্জনের জন্য নারী চাকরি বা ব্যবসা করুক—এ নীতিতে আমার বিশ্বাস নেই। …মেয়েদের বিদ্যালয়েও ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তন করার একমাত্র অর্থ হচ্ছে আমাদের অসহায় অবস্থার মেয়াদ বৃদ্ধি করা।’ (বোম্বাই ভগ্নী সমাজের সভাপতির অভিভাষণ; ১৯১৮)
‘…গৃহস্থলীর ব্যাপারে ও শিশুপালন এবং তাদের শিক্ষা সম্বন্ধে নারীর অধিকতর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।’ (ঐ) এবং মাধ্যমিক শিক্ষার সময় মেয়েদের ‘ইংরেজি শেখানোর অর্থ তাদের মেরে ফেলা।’ ‘আমার মতে মেয়েদের সংস্কৃত শেখানো উচিত।’ ‘হিন্দুধর্মের মূলনীতি এত প্রচ্ছন্ন যে কিভাবে এ ধর্ম শেখানো যেতে পারে হঠাৎ তা বলা যায় না। তবে মোটামুটি এই কথা বলা যায় যে, গীতা রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবতকে হিন্দুরা সবাই শ্রদ্ধা-দৃষ্টিতে দেখেন এবং এই সব ধর্মগ্রন্থের আধ্যাত্মিক জ্ঞানের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের হয় তাহলে যথেষ্ট কাজ হবে মনে হয়।’ (আত্ম্যোদ্ধার)
(তুলনীয়–হিন্দুমৌলবাদীদের অনুমোদিত ও ক্ষমতাশীল থাকার সময় উত্তর প্রদেশে কিছুদিন আগেও সরকারীভাবে উৎসাহিত পাঠ্যপুস্তকের কিছু অংশ–’নারীমুক্তি শুরু হয়েছে। এই কিছুদিন আগেও মেয়েরা চার দেওয়ালের মধ্যে থাকত ও সংসারকে ঐক্যবদ্ধ করে রাখত। এখন তারা কাজে বেরুচ্ছে-পেছনে ফেলে যাচ্ছে তার সংসারকে। নারী-স্বাধীনতা পরিবারে এক ধরনের চাপ-এর সৃষ্টি করে এবং অনেক পরিবার এই স্বাধীনচেতা, মুক্ত মনোভাবের জন্য ভেঙ্গে যায়।.’
‘যে সব আইন নারীদের অধিকার দিয়েছে সেগুলিও পারিবারিক বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। হিন্দু বিধবা পুনর্বিবাহ আইন, ১৯৫৬; হিন্দু নারীদের সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কিত আইন, ১৯৩৭; বিশেষ বিবাহ আইন, ১৯৫৪; হিন্দু বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ আইন, ১৯৫৫-এ সবগুলিই মেয়েদের অবস্থানকে উন্নত করেছে। মেয়েরা তাদের বাবা-মোর সম্পত্তির উত্তরাধিকারীও হচ্ছে। মেয়েদের অনুকূলে সরকারের শুরু গ্রগতিশীল আইনগুলির সমধিক ফল হচ্ছে পরিবারে উত্তল ও বিবাদের সৃষ্টি।’
নাৎসীদের প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলসের এ ব্যাপারে মত ছিল, ‘মেয়েদের দায়িত্ব হচ্ছে নিজেরা সুন্দরী থাকা ও সন্তান ভূমিষ্ট করা…’
হিটলার-এর বক্তব্য ছিল, ‘মেয়েদেরও তাদের নিজস্ব যুদ্ধক্ষেত্ৰ আছে। দেশের জন্য প্রত্যেকটি শিশুর জন্ম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, দেশের স্বার্থে সে তার নিজস্ব লড়াই চালিয়ে যায়।’–ফ্রন্টলাইন, ৯.৪.৯৩ থেকে সংগৃহীত)
কিন্তু হিটলার বা হিন্দুমৌলবাদীর হুবহু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গান্ধীর মধ্যে নেই। তাই দেখি তিনি এও বলেন যে,–
‘পুরুষদের মত নারীদের ভিতর নিরক্ষরতার কারণ আলস্য ও জাড্য নয়। যে হীন অবস্থার বোঝা নারীকে স্মরণাতীত কাল থেকে অন্যায়ভাবে নিচিপষ্ট করে মারছে, নারীর বর্তমান অবস্থার প্রত্যক্ষ কারণ তাই। পুরুষ নারীকে তার কর্মসহচরী ও অর্ধাঙ্গীর মর্যাদা দেওয়ার পরিবর্তে তাকে গৃহস্থলীর নীরস কৃত্য সম্পাদনাযন্ত্র ও সম্ভোগপত্রে পরিণত করেছে। ফলে সমাজ প্রায় পঙ্গু হয়ে পড়েছে। নারীকে অতি সঙ্গত কারণেই জাতির মাতা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাদের প্রতি আমরা যে মহা অবিচার করেছি, তাঁদের ও আমাদের উভয়ের খাতিরে তার নিরাকরণ করতে হবে।’ (হরিজন; ১৮.২৯৩৯)
এবং এও তাঁর বলিষ্ঠ উচ্চারণ যে, ‘আমি যে বিশেষ কোন বর্ণের অন্তর্গত একথা তো আমি বহুদিনই ভুলিয়া গিয়াছি। কাজেই আমি নিজেকে ভাঙ্গী বলিয়া অভিহিত করিতে এবং সেইমত কাজ করিতে আনন্দ পাই। সমাজকে তো উচ্চনীচ স্তরে ভাগ করা চলে না। তাহা ছাড়া বৰ্ণহিন্দু সমাজ যদি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যদের লইয়াই হয় তাহা হইলে তাহারা তো শোচনীয়ভাবে সংখ্যালঘু। বৃটিশ শাসনের অবসানে ভারতে যখন স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন উচ্চবর্ণ হিসাবে এই তিনশ্রেণীর বিলোপ সাধন ঘটিবে। সকল অসামাই তখন অতীতের কাহিনী বলিয়া গণ্য হইবে এবং তখনই তথাকথিত দলিত শ্রেণী তাহাদের স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হইবে।’ (নোয়াখালি ডাইরি, ১৯৪৭)।
‘বৃটিশ শাসনের অবসানে ভারতে’ কি হয়েছিল তা অজানা নয়। গান্ধীর ভবিষ্যদবাণী সত্য হয়নি। উচ্চ তিনবর্ণ এখনো রয়েছে। এবং সত্যি কথা বলতে কি এমন সোনার পাথর বাটি সম্ভবও নয়। তিনি নিজে সারাজীবন ধরে নিজেকে, উচ্চবর্ণের না হোক, হিন্দু বলে মনে করবেন এবং হিন্দুধর্মের ধর্মগ্রন্থগুলি পড়ানোর সুপারিশ করবেন (-রামায়ণ, মহাভারত বা ভাগবতের মত যেসব গ্ৰন্থ বৰ্ণাশ্রমের ব্যাপক প্রচারে ভরা,)—আর শেষ সময়ে আশা করবেন বৰ্ণভেদ লুপ্ত হবে, এটি যে হওয়ার নয় তা সহজবুদ্ধিতেও বোঝা যায় এবং এইভাবেই সম্ভব হয় নি হিন্দুমুসলমান বিভাজনকে আটকাতে, এদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের উত্থানকে রুখতে। এই উত্থানের পেছনে গান্ধী তথা কংগ্রেসের ভূমিকা,-’তাদের সাম্প্রদায়িক না বলা গেলেও এবং তারা ধর্মনিরপেক্ষ ভারত গড়ার কথা বল্লেও, ছিল।
তাই দেখি তাঁর উত্তরসূরী শ্ৰীমতী ইন্দিরা গান্ধী হিন্দু মৌলবাদীদের উৎসাহিত করছেন। (‘বিশেষত ১৯৮০ সালের পর থেকে শ্ৰীমতী ইন্দিরা গান্ধী হিন্দু ভোটের উপর নির্ভর করতে শুরু করলেন, কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সংখ্যালঘু ভোটের উপর তিনি আর ভরসা করতে পারবেন না। ১৯৮১ সালে মীনাক্ষীপুরমে কয়েকটি হরিজন পরিবার ধর্মান্তরিত হয়। এই ঘটনার পর তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদ গঠন ও তার প্রসারকে প্রচ্ছন্নভাবে উৎসাহ দিতে লাগলেন। হিন্দুদের ভিতর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রভাব বাড়তে লাগল, বাড়তে লাগল তাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা। এই ব্যাপারটিও শ্ৰীমতি গান্ধীকে আরো বেশি ঠেলে দিল হিন্দু ভোট জয়ের লক্ষ্যে এগনোর পথে।’-আসগর আলি ইঞ্জিনীয়ার-এর প্রবন্ধ ‘বন্ধ হোক এই পাগলামি’) এমনকি আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পৃষ্ঠপোষক (যান্ত্রিক!) হিসেবে প্রচারিত রাজীব গান্ধীও অপরিণামদর্শীর মত, নিতান্তই সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে মুসলিমও হিন্দুমৌলবাদীদের উৎসাহিত করেছেন ও তোষণ করেছেন। শাহবানু মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায় মুসলমান মৌলবাদীদের ক্ষুব্ধ করলে তাদের আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করে সেই রায়কে নাকচ করিয়ে ১৯৮৬-এর মে মাসে মধ্যযুগীয় মুসলিম মহিলা বিল সংসদে পাশ করানো হল। সংসদে বিলটি ২৫শে ফেব্রুয়ারী পেশ করার আগে হিন্দুমৌলবাদীদের খুশি করতে ফৈজাবাদ জেলা আদালতের মাধ্যমে বাবরি মসজিদের দরজা হিন্দুদের জন্য খুলে দেওয়া হল। তার আগের ও পরের ইতিহাস অনেকের জানা, এখানে বিস্তারিত জানানোরও প্রয়োজন নেই। কিন্তু অমৌলবাদীর মুখোশ পরা ব্যক্তিদের হাতেও ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার ও মৌলবাদের তোষণ কেমন জঘন্যভাবে হতে পারে—এসব তারই ইতিবৃত্ত। এগুলিকে ‘পাগলামি’ বলা অনেকটা ক্ষমা করে দেওয়ার সামিল। মৌলবাদকে সস্তুষ্ট ও উৎসাহিত করতে এ ধরনের কাজ ও কথাবার্তা মৌলবাদী ক্রিয়াকাণ্ডেরই একটি দিক। ঈশ্বরও ধর্ম-বিশ্বাসের দ্বারা নিষিক্ত হয়ে গান্ধীবাদী কংগ্রেসী রাজনীতির মধ্যে হিন্দু মৌলবাদ একদা এভাবেই পরিপুষ্ট হয়েছে।
অন্যদিকে একসময় বামপন্থীদের মত জয়প্রকাশ নারায়ণও হিন্দু মৌলবাদীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৭৩-৭৪ সালে তাঁর নেতৃত্বে ইন্দিরা সরকারবিরোধী আন্দোলনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ ও ভারতীয় জনসঙ্ঘ তার সহযোগী হয়ে যায়। ১৯৭৪-এর ডিসেম্বরে আর এস এস-এর সরীসংঘচালক বালাসাহেব দেওরস। জয়প্ৰকাশকে ‘সন্ত’ বলে অভিনন্দিত করেছেন। আর ১৯৭৫-এর মার্চে জয়প্রকাশও প্রকাশ্যে ফ্যাসিস্ট রাজনীতির অভিযোগ থেকে জনসঙ্ঘকে মুক্তি দেন।(১) ১৯৭৫-এর ২৫শে জুন (জরুরী অবস্থা ঘোষণার ঠিক আগে) লোক সংঘর্ষ সমিতি গড়া হলে প্রাক্তন আর এস এস প্রচারক ও শীর্ষস্থানীয় বিজেপি নেতা নানাজি দেশমুখকে তার সম্পাদক করে দেওয়া হয়। ঐ সময় ধর্মীয় মৌলবাদীদের সঙ্গে এ ধরনের আঁতাত কতটা যুক্তিযুক্ত ছিল তার বিচার করার সুযোগ ও সামৰ্থ্য এখানে নেই। তবে এটুকু স্পষ্ট যে, দেশের মানুষের কাছে তাদের ক্রমশ গ্রহণযোগ্য করে তোলার এবং তাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে এধরনের পদক্ষেপের কিছু ভূমিকা আছেই। স্বৈরতন্ত্র, দক্ষিণপন্থা ইত্যাদির চেয়ে ধর্মীয় মৌলবাদীরা যে তবু গ্রহণযোগ্য—এই ধরনের একটি সর্বনাশা ধারণাও তা তৈরী করতে পেরেছে। এখন তার ফল ফলতে শুরু করেছে।
আমাদের প্রতিবেশী বাংলাদেশে আরো সুস্পষ্টভাবে ইসলামী মৌলবাদীরা তথাকথিত অ-মৌলবাদী রাজনৈতিক শক্তিদের দ্বারা উৎসাহিত ও পরিপুষ্ট হয়েছে। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষেত্রে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ-এর ভূমিকা সর্বজনবিদিত। পাকিস্থানী শাসন মুক্ত হয়ে বাংলাদেশের জন্ম সারা পৃথিবীর শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষদের মধ্যে যেমন, তেমনি ভারতে, বিশেষত ভারতীয় বাঙালীদের মধ্যে একটি আবেগ ও আশার সঞ্চার করেছিল। এও হয়তো আশা করা গেছিল যে, সাম্প্রদায়িক মুসলীম লীগ-এর উত্তরাধিকারী মৌলবাদী জামাতে ইসলামীর কারাল গ্রাস থেকে বাংলাদেশের জনগণ মুক্ত হতে পারবেন। কিন্তু এ ছিল আকাশকুসুম কল্পনা।
আওয়ামী লীগ আসলে ছিল মুসলিম লীগ থেকে ভেঙ্গে আসা একটি অংশের নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। প্রথমে এর নাম ছিল ‘আওয়ামী মুসলিম লীগ, পরে নাম পাল্টে হয় ‘আওয়ামী লীগ’। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে এভাবে নাম পাল্টালেও নেতৃত্বের অধিকাংশই তাঁদের সাম্প্রদায়িক ইসলামী চরিত্র এবং নিজেদের গোঁড়া মুসলিম পরিচয়কে অক্ষুন্ন রাখেন। এই অবস্থায় স্বাধীন ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিলেও অবশেষে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের দোসরে পরিণত হওয়ার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার ভালভাবেই ছিল।
এরই প্রতিফলন ঘটে ঐ আওয়ামী লীগের আমলে অবৈজ্ঞানিক ধর্মীয় মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার বাড়বাড়ন্তের মধ্যে; তাদের সংখ্যা বাড়ানো হয়, মাদ্রাসা শিক্ষা খাতে ব্যয়বৃদ্ধিও করা হয়। এবং আরো ভয়াবহ হল, আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭১এর রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও ঘাতক দালালদের প্রতি নমনীয় নীতিও গ্ৰহণ করে; পাশাপাশি বামপন্থী কর্মীদের উপর নিপীড়ন নামায়, তাদের হত্যাও করতে থাকে লালবাহিনী, রক্ষী বাহিনী ইত্যাদির মাধ্যমে। মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা শুরুর দিকে বলা হলেও, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলেই নতুন করে টেলিভিশন রেডিওতে ‘খোদা হাফেজ’ বলা চালু হয়, সরকারীভাবে গণভবনে ধর্মীয় মিলাদ অনুষ্ঠানও করা হয়। তবু আওয়ামী লীগ বিভিন্ন ধর্মীয় দলসহ জামাতে ইসলামীকে বেআইনী ঘোষণা করেছিল।
কিন্তু পরবর্তীকালে সামরিক আইন প্রশাসক জিয়াউর রহমানের আমলে (১৯৭৮) জামাতে ইসলামীর উপর এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে তাদের প্রকাশ্যে ও আইনসঙ্গতভাবে একটি রাজনৈতিক দল হিসাবে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হল। ধর্মীয় মৌলবাদী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও তাত্ত্বিক লড়াই নয়, তাদের রাজনৈতিকভাবে মর্যাদা দেওয়া ও প্রতিষ্ঠিত করার কাজই করা হল। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বি এন পি) এই জিয়াউর রহমানেরই রাজনৈতিক সংগঠন। আওয়ামী লীগ সদ্যপ্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধ্বংস করে ধর্মীয়া (ইসলামী) প্রভাব যেমন ঢোকানো শুরু করেছিল, এই জিয়াউর রহমানের আমলে তারই ধারাবাহিকতায় সংবিধানেই ‘বিসমিল্লাহ রাহমানির রাহিম’ সংযোজন করা হল। ব্যক্তিগত বিশ্বাসের স্তর থেকে ধর্মকে এইভাবে রাষ্ট্ৰীয় ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রসারিত করার পরোক্ষ ফলাফলই হোল ধর্মীয় মৌলবাদীদের নৈতিক জয় ঘোষণা করা এবং তাদের উৎসাহিত করা।
আর এর পরে এরশাদের আমলে তো বামপন্থীরাও সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সহযোগী হিসেবে গ্রহণ করে পরোক্ষভাবে উঠে পড়ে লেগে যায় মৌলবাদী জামাতে ইসলামীর রাজনৈতিক প্ৰতিষ্ঠাকে শক্তিশালী করতে। একইভাবে পশ্চিমবাংলাতেও বামপন্থীরা ১৯৮৫ সালে কলকাতা পুরসভার নির্বাচনের পর ত্রিশঙ্কু ফলাফলের সময় বিজেপি-র সমর্থন নিয়ে (অর্থাৎ তাদের সহযোগী বা বন্ধু হিসাবে স্বীকার করে নিয়ে) পুরসভা গঠন করে। তবে বাংলাদেশের বামপন্থীদের সঙ্গে পশ্চিমবাংলার বামপন্থীদের একটি বড় তফাৎ হচ্ছে–এখানকার তথাকথিত বামপন্থীদের বিপুল অংশ আদৌ ধর্মমোহমুক্ত না হলেও,-প্রকাশ্যে বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদকদের মত নির্বাচনী পোস্টারে (১৯৯১) ‘আল্লাহো আকবর’-এর সমগোত্রীয় (‘জয়শ্ৰীরাম’ কিংবা ‘ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, কারণ তিনি সত্য’?) শ্লোগান কখনোই দেন নি। তাঁদের নেতার মৃত্যুতে পার্টি অফিসে ধর্মীয় শ্ৰাদ্ধানুষ্ঠান করার কথাও তারা ভাবতে পারেন না, যেমন বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি অফিসে মিলাদ অনুষ্ঠানের কথা জানা আছে। এছাড়া অস্তুত বর্তমানে পশ্চিমবাংলার বামপন্থীরা বিজেপি-র মত হিন্দু মৌলবাদীদের থেকে শত হাত দূরে থাকার চেষ্টা করেন। যেমন ১৯৯৫-এ কলকাতা পুরসভার নির্বাচনের পর, ১০ বছর আগেকার ঐ ত্রিশঙ্কু ফলাফলের পুনরাবৃত্তি ঘটলেও তারা (এবং কংগ্রেসীরাও) স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন যে, আর যাই হোক নির্বাচিত দুই বিজেপি সদস্যার সমর্থন র্তারা পুরসভা গঠন করতে আদৌ গ্ৰহণ করবেন না। স্বস্তিকর ও সুস্থ এই ব্যাপারটির মধ্যে আন্তরিকতা কতটা, আর রাজনৈতিক সুবিধাবাদ কতটা তার বিচার করা মুস্কিল,-বিশেষত যখন মুসলিম লীগ ও বিজেপিদের সঙ্গে তাদের রাতনৈতিক আঁততের পূর্ব ইতিহাস অজানা নয়।
ধর্মের সঙ্গে, ধর্মীয় রাজনৈতিক সংগঠন এবং ধর্মীয় মৌলবাদী সংগঠনের সঙ্গে এই ধরনের সুবিধাবাদী আঁতীতের পেছনে নিছক সুবিধাবাদ ছাড়াও ধর্মের প্রতি এক ধরনের মমত্ববোধ, ধর্মকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার প্রবণতা, নিজেদের সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীভিত্তি ইত্যাদিও কাজ করে।
ধর্মীয় মৌলবাদীদের এখানে এই একটি বড় সুবিধা। বামপন্থীদের স্রোতের বিরুদ্ধে হাঁটতে হয়, বহু শত বছরের ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের জনবিরোধী চরিত্রটি উন্মোচিত করে বস্তুবাদী দর্শনকে তুলে ধরতে হয় এবং কোন অতিপ্রাকৃতিক ঐশ্বরিক শক্তির উপর নির্ভর করে নয়, মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আত্মনির্ভরতায় বলিষ্ঠ করতে হয়। একাজে এখনো সঙ্গী যেমন কম, তেমনি নিজেদের সহযোগী হিসেবে মনে করা ব্যক্তিদের মধ্যে দোদুল্যমানতাও বেশি। অন্যদিকে ধর্মীয় মৌলবাদীরা হাঁটে স্রোতের দিকেই। যে অলীক ঐশ্বরিক কল্পনা ও মায়াময় ধর্মবিশ্বাসকে আঁকড়ে রেখে বিপুল সংখ্যক মানুষ ভিত্তিহীন সাহসের সন্ধান করে, সেই কল্পনা ও বিশ্বাসকে আরো তীব্র হিংস্রভাবে সুসংহত করে মৌলবাদীরা। আর প্রচলিত এই স্রোতের গাড ধরে এগোেনর পথে তারা কখনো কখনো সঙ্গী হিসেবে পেয়ে যায় বামপন্থী বা কম্যুনিষ্ট, গণতান্ত্রিক বা ধর্মনিরপেক্ষ হিসেবে পরিচিত ও প্রচারিত এবং মৌলবাদের ছাপ্লামুক্ত মানুষদেরও,-মূলত তাদের অন্তর্নিহিত ধর্মবিশ্বাসের কারণে।
বামপন্থী বা কম্যুনিষ্টসহ এ ধরনের মানুষেরা নানা জটিল সময়ে ধর্মীয় মৌলবাদীদের সাহায্য করলেও, কম্যুনিজমকে সামান্য সাহায্য করা দূরের কথা ধর্মীয় মৌলবাদীরা কিন্তু তীব্রভাবে এই কম্যুনিজমের বিরোধী। কি আমেরিকায় ফান্ডামেন্টালিস্টরা, কি হিন্দু ও মুসলিম মৌলবাদীরা সবার ক্ষেত্রেই এটি অন্যতম সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও ধর্মের অন্তঃসলিলা চোরাস্রোতের কারণে তারা অমৌলবাদী হিসেবে চিহ্নিত আবামপন্থীদের থেকে তো বটেই, এমনকি? বামপন্থীদের থেকেও বা তার আপাত শত্রুদের কাছ থেকেও সহযোগিতা আদায় করে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে।
মানসিকতা ও কিছু কাজকর্মে একনায়কতন্ত্র বা ম্বৈরতান্ত্রিক আচরণ মৌলবাদের আরেকটি বিশেষ চারিত্রিক দিক হিসেবে প্রতিফলিত হয়। এটির উৎস আসলে বিশেষ একটি ধারণার প্রতি দ্বিধাহীন বিশ্বাস থাকার কারণে। বাইবেল, কোরান বা বেদ ঐগুলি ঐশ্বরিক ও সর্বোত্তম, এদের সামান্য পরিবর্তন করা বা অবমাননা, সমালোচনা করাও ধর্মবিরোধী–এ ধরনের বিশ্বাস থাকলে নিজের কাজের ক্ষেত্রেও এমন গোঁড়ামির বহিঃপ্রকাশ ঘটতে বাধ্য এবং তার ফলশ্রুতিতে নেতৃত্বের প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্যের পরিবেশও সৃষ্টি হয়। মূলগত ঐ গোঁড়ামির কারণে নেতৃত্বেরও সামান্য সমালোচনা করার মানসিকতাই ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়। নেতা তখন ঈশ্বরের এবং তার কথা (বাণী!) ধর্মগ্রন্থের সমগোত্রীয় হয়ে দাঁড়ায়।
হিটলার-গোয়েবলসরাও নিজেদের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশুদ্ধ আর্যরক্তের তত্ত্বে গভীরভাবে বিশ্বাস করত। তাদের নীতিই ছিল—একটি মিথ্যাকে বারবার বিশ্বাসযোগ্যভাবে বলা। এই বিশ্বাস ও এই মিথ্যার স্বার্থে তারা কি পাশবিক ক্রিয়াকাণ্ড করেছে তা আজ কারোর অজানা নয়।
ধর্মীয় মৌলবাদীরাও ফ্যাসীবাদীদের মত প্রায় একই ঢঙে কাজ করে। আর কোন রাজনৈতিক দলের মধ্যেও একই ধরনের স্বৈরতান্ত্রিকতা ও অগণতান্ত্রিকতা কাজ করতে পারে। কিন্তু সাধারণভাবে রাজনৈতিক দলের মধ্যে বা অন্য কোন গণতান্ত্রিক সংগঠনের মধ্যে এই প্রবণতা সংগঠনের অসুস্থতা ও ক্ষয়ের লক্ষণ। কিন্তু রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক মৌলবাদী সংগঠনের ক্ষেত্রে এটি তার অবধারিত বৈশিষ্ট্য। এবং এ কারণে হিটলারীয় দর্শন থেকে শিক্ষালাভ করার কথা দ্বিধাহীনভাবে উচ্চারণ করে তারা। যেমন করেছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের এস এম গোলওয়ালকর তার ‘উই আর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইনড’ (১৯৩৮) গ্রন্থে – ‘জার্মানদের জাতিত্বের গর্ব আজ মুখ্য আলোচ্য বিষয় হয়ে পড়েছে। নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতিকে কলুষমুক্ত করতে জার্মানি গোটা বিশ্বকে স্তম্ভিত করে সেমেটিক জাতি-ইহুদিদের দেশ থেকে বিতাড়ন করেছে। জাতিত্বের গর্ব এখানে তার সর্বোচ্চ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। জার্মানি এটাও প্রমাণ করেছে যে, নিজস্ব ভিন্ন শিকড় আছে এমন জাতি বা সংস্কৃতির একসঙ্গে মিশে একটি পূর্ণাঙ্গ সত্তা তৈরী করা অসম্ভব। এই শিক্ষা হিন্দুস্তানে আমাদের গ্রহণ করা এবং তার থেকে আমাদের উপকৃত হওয়া প্রয়োজন।’
মুসলিম মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাও একই কথা বলে; যেমন, ১৯৪১এর মার্চ মাসে সিন্ধু-র মুসলিম লীগ নেতা এম. এইচ. গজদর করাচীর সভায় বলেছিলেন, ‘হিন্দুরা যদি ঠিকমত ব্যবহার না করে তবে জার্মানী থেকে ইহুদিদের যেমন দূর করে দেওয়া হয়েছে, তাদেরও তাই করতে হবে।’ ফ্যাসিবাদ মৌলবাদের গুরুদেব!
গোলওয়ালকর অন্যত্র আরো বলেছিলেন,–‘আমাদের দেশের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস এই কথাই বলে যে সমস্ত কিছু করেছে একমাত্র হিন্দুরা। এর অর্থ এই যে কেবল হিন্দুরাই এই মাটির সন্তান হিসেবে বসবাস করেছে।’
এবং তাই— ‘…হিন্দুস্থানের সমস্ত অহিন্দু মানুষ হয়। হিন্দু ভাষা ও সংস্কৃতি গ্ৰহণ করবে, হিন্দু ধর্মকে শ্ৰদ্ধা করবে ও পবিত্র বলে জ্ঞান করবে, হিন্দু জাতির গৌরব গাথা ভিন্ন অন্য কোন ধারণাকে প্রশ্রয় দেবে না, অর্থাৎ তারা শুধু তাদের অসহিষ্ণুতার মনোভাব এবং এই সুপ্রাচীন দেশ ও তার ঐতিহ্যের প্রতি অবজ্ঞার মনোভাবই ত্যাগ করবে না, এর প্রতি ভালোবাসা ও ভক্তির মনোভাব তৈরী করবে। এক কথায় তারা হয়। আর বিদেশী হয়ে থাকবে না, না হলে সম্পূর্ণভাবে হিন্দু জাতির এই দেশে তারা থাকবে অধীনস্থ হয়ে, কোনও দাবি ছাড়া, কোনও সুবিধা ছাড়া এবং কোনও রকমের পক্ষপাতমূলক ব্যবহার ছাড়া। এমনকি নাগরিক অধিকারও তাদের থাকবে না।’’
নামাজ না পড়া, মদ্যপানে অভ্যস্ত মহম্মদ আলি জিন্না-ও আসলে কতটা ইসলামে আস্থা রাখতেন, ঐ বিতর্ক থাকলেও, রাজনৈতিক শ্রেণী স্বার্থে তিনিও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে ব্যবহার করতে গিয়ে ১৯৪১ সালে মন্তব্য করেছিলেন, ‘মুসলিমদের ব্যাপক অংশ এখন সহস্ৰাধিক বছর ধরে একটি ভিন্ন জগত, একটি ভিন্ন সমাজ, একটি ভিন্ন দর্শন ও একটি ভিন্ন অবস্থায় জীবন নির্বাহ করছে।’ সব শেয়ালের একই রা!
বর্তমানের হিন্দু মৌলবাদী সমস্ত সংগঠনেরও মূলকথা এইই।** এই সংকীর্ণতম, অগণতান্ত্রিক, অনৈতিহাসিক মিথ্যাচারকে বারংবার বলে বলেই তারা দেশের বিপুল সংখ্যক হিন্দু ও ইসলাম ধর্মবিশ্বাসী সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করেছে। এবং করছেও, যেমন করেছিল হিটলার ও তার সঙ্গীসাথীরা।
এবং তাদেরই মত এরাও কঠোর সাংগঠনিক শৃঙ্খলায় কর্মীদের শিক্ষিত ও অভ্যস্ত করে। যেমন আর এস এস-এর নতুন সদস্য এলে তাদের নিয়মিত এই প্রশ্ন করা হয়,-’যদি তোমার অধিকারী’ তোমাকে কুঁয়োয় ঝাপ দিতে বলে, তুমি কি করবো?’ প্রত্যাশিত উত্তর হল, ‘আমি তক্ষুণি ঝাপ দেব।’ কোন প্রশ্ন নয়, কোন অজুহাত নয়। কেউ উত্তর দিতে দ্বিধা করলে তাকে বিদ্রুপে জর্জরিত করা হয়। অন্যদিকে আর এস এস-এর নিয়মিত অনুষ্ঠানের একটি হচ্ছে সেপ্টেম্বরের ব্যাসপূজা। এই সময় গেরুয়া পতাকার পূজা করা হয় এবং সদস্যরা নিজেদের পরিচয় গোপন রেখে অর্থ দান করেন। এই দান থেকেই সংগঠনের ভাণ্ডার পরিপুষ্ট হয়, কিন্তু তার কোন রসিদ দেওয়া হয় না, কোনও নথিও রাখা হয় না। সব মিলিয়ে কি সাংগঠনিক, কি আর্থিক সমস্ত দিক থেকেই নেতৃত্বের চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা হয়। নেতৃত্বকে কোনভাবে প্রশ্ন করা, বিচার করা, সন্দেহ করার মানসিকতাটিকেই ধ্বংস করা হয়। এই মানসিকতা না থাকাটাই মূল ধর্ম, ধর্মগ্রন্থ ও ধর্মীয় নেতৃত্বকে অন্ধভাবে মেনে চলার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। হিটলারের নাৎসিবাহিনীও একইভাবে পরিচালিত হত। পাকিস্তানে জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মওদুদীও একই হিটলারীয় কায়দার কথা বলেছেন। তাঁর মতে ইসলামী রাষ্ট্রে থাকবে শুধু একটিমাত্র দল, হিজাব-ই-আল্লা (অর্থাৎ the party of God)। কোরান শরীফেও বলা হয়েছে, ‘তারা কি জানে না যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে তার জন্য আছে জাহান্নামের আগুন, সেথায় সে স্থায়ী হবে, উহা ভীষণ লাঞ্ছনা।’ (সূরা ৯ আয়াত ৬৩) কিংবা ‘এবং যারা অবিশ্বাস করে ও আমার নিদর্শন সমূহে মিথ্যারোপ করে, তারাই নরকের অধিবাসী, সেখানে সর্বদা অবস্থান করবে।’ (সূরা ২, আয়াত ৩৯) অর্থাৎ অবিশ্বাস করার কোন উপায় নেই। সব মিলিয়ে প্রতিটি ধর্মীয় মৌলবাদী ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে একনায়কতন্ত্রী প্রবণতার বহিঃপ্রকাশ ঘটছেই।
ব্যাপারটিকে ফ্যাসিস্ট কায়দার সঙ্গে তুলনা করা যায়। কঠোরভাবে কম্যুনিজম বিরোধী, হিংস্র জাতীয়তাবাদী এই ফ্যাসিস্টদের মতই ধর্মীয় মৌলবাদীরাও বিশেষ ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা, কাজেকর্মে হিংস্র এবং মূলগতভাবে কম্যুনিজম বিরোধী। কিন্তু স্পষ্টতই আগেকার ঐ ফ্যাসিস্টদের থেকে এখনকার ধর্মীয় মৌলবাদীদের প্রধান ও বীভৎস পার্থক্য হল, দ্বিতীয়রা ফ্যাসিস্ট কায়দার সঙ্গে ধর্মের ও ধর্মীয় বিভাজনের মত একটি কৃত্রিম ও নিছক বিশ্বাসগত দিকের সম্পূক্ত সংমিশ্রণ ঘটায়। এই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের কারণে ইরানের মুসলিম মৌলবাদীরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে,
‘এই ব্যবস্থার ও মুসলমানদের ন্যায়পরায়ণ ইমাম (খোমেনি)-র বিরোধিতা যে করে, তার উপযুক্ত শাস্তি মৃত্যু। তেমন কোন লোক গ্রেপ্তার হলে তাকে হত্যা করতে হবে। সে আহত হলে তাকে আরো আহত করতে হবে, যতক্ষণ না তার মৃত্যু হয়। যে বর্তমান ব্যবস্থা ও ন্যায়বান ইমামের বিরুদ্ধে, তার একমাত্র দণ্ড মৃত্যু।’ (১৯৮১ তে জুম্মাবারে ইরানের পাবলিক প্রসিকিউটার আয়াতোল্লা মুসাভি তাবরিজির নামাজ-কালীন বক্তৃতার অংশ।) ১৯৯০-এর অক্টোবরে অযোধ্যা ও ফৈজাবাদের বাড়ী ও মন্দিরগুলির দেওয়াল লিপিতে ‘হিন্দুদের বাধ্যতামূলক ধর্মীয় কাজ যারা গোহিত্যা করে তাদের হত্যা করা’ ধরনের নির্দেশও ওই মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ।
ফ্যাসিস্টদের মত এদের দ্বিধাহীন নিরলস কম্যুনিজমবিরোধিতার কথা সর্বজনবিদিত। ১৯৪৮ সালে মহাত্মা গান্ধী হত্যার পর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, আর এস এস নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। তাদের উপর থেকে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার অনুরোধ করে গোলওয়ালকার নেহেরু ও প্যাটেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাদের কাছে লেখা ২৪শে সেপ্টেম্বর এর চিঠিতে তিনি এ ব্যাপারে সব চেয়ে জোর দেন যে,–দেশে কম্যুনিজম-এর প্রসার আটকাতে গেলে আর.এস.এস.কে খোলাখুলি কাজ করতে দেওয়া উচিত। বাম, জাভা, ইন্দোচীন ইত্যাদি। পার্শ্ববতী দেশের বিপজ্জনক ঘটনাবলীর উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘আপনার সরকারি ক্ষমতা এবং আমাদের সংগঠিত সাংস্কৃতিক শক্তি এক হলে আমরা এই বিপদের (কমিউনিজমের প্রসারের) অবসান করতে পারব।’ নেহরুরা অবশ্য এই যুক্তিতে টলেননি, কিন্তু কম্যুনিজম বিরোধিতায় আর এস এস চক্রের চরম আগ্রহ ও নীতিগত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে কোন সন্দেহ থাকে না। বাংলাদেশেও মুসলিম মৌলবাদী জামাতে ইসলামীরা হিন্দুদের থেকে কম্যুনিষ্টদের ও বামপন্থা তথা মার্কসীয় দর্শনকে অনেক বেশি আক্রমণের লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে। আমেরিকার ফান্ডামেন্ডালিস্টদের থেকেই এই ধারা চলছে। আসলে আদর্শ হিসেবে কমিউনিজমের তথা বস্তুবাদী দর্শনের তীব্র কঠোর ও নিরলস বিরোধিতা না করলে এই মৌলবাদী মানসিকতাকে টিকিয়ে রাখা ও তার প্রসার করা যাবে না। ফ্যাসিস্টদের হিংস্র কম্যুনিজম বিরোধিতার সঙ্গে মৌলবাদীদের কিছু সাযুজ্যও তাই চোখে পড়ে।
মৌলবাদ-মৌলবাদী প্রসঙ্গে আরেকটি কথাও বলা দরকার। মৌলবাদ একটি সাধারণ দৃষ্টিঙ্গিী হলেও এবং খৃস্ট বা হিন্দু বা ইসলামী মৌলবাদী বলে উচ্চারণ করলেও, একই ধর্মের মৌলবাদীরা যে গভীরভাবে ঐক্যবদ্ধ তা নয়। ধর্মের প্রসঙ্গে তাদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য থাকলেও এবং একই ধর্মের মৌলবাদীদের মধ্যে একটি সাধারণ যোগসূত্র থাকলেও, নানা স্বার্থের সংঘাতের কারণে এবং ধর্মের মূল কোনটি তা নিয়ে বিতর্কের কারণে তাদের মধ্যে অনৈক্যও থাকে। আমেরিকার খৃস্টীয় ফান্ডামেন্ডালিস্টরা বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন সংস্থা কিভাবে গড়ে তুলেছিল তা আমরা আগেই দেখেছি। ইরান ও পাকিস্থানে ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম হলেও দু’দেশের মৌলবাদীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে কিছু তফাৎ আছে। ইরানে মৌলবাদের একটি বড় ভূমিকা ছিল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতায়। পাকিস্থানে আবার মৌলবাদীরা সাম্রাজ্যবাদনির্ভর। আরবে ইসলামী মৌলবাদের মধ্যে রাজার মৌলবাদ’ ও ‘র্যাডিক্যাল মৌলবাদী হিসেবে দুটি পৃথক ধারা লক্ষ্য করা যায় এবং তাদের মধ্যে সংঘর্ষও ঘটে অর্থাৎ ইসলামী মৌলবাদের সঙ্গে ইসলামী মৌলবাদের সংঘর্ষ। র্যাডিক্যাল ইসলামী মৌলবাদীরা কয়েক বছর আগে এই ধরনের একটি সংঘর্ষের ফলশ্রুতিতে কিছুক্ষণের জন্য কাবা দখলও করে নিয়েছিল। হিন্দু মৌলবাদীদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকসঙ্ঘ (আর.এস এস) সাংগঠনিক, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভি এইচ পি) সামাজিক ও এককালের ভারতীয় জনসংঘ (বি জে এস)-এর রাজনৈতিক উত্তরাধিকারী ভারতীয় জনতাপার্টি (বি জে পি) ‘রাজনৈতিক দিকগুলি প্ৰধানত দেখাশুনা করে এবং বিজেপি-র প্রাক্তন সহ সভাপতি সুন্দরসিং ভাণ্ডারির মতে তিনটিই স্বক্ষেত্রে স্বাধীন, তিনটিই জাতীয় সংগঠন, কিন্তু একই হিন্দুত্বের সংস্কৃতি দ্বারা পরিচালিত। এদের সঙ্গে শিবসেনা সহ আরো বহু সংগঠন (যেমন অখিল ভারত বিদ্যাখী পরিষদ, রাষ্ট্র সেবিকা সমিতি, দুর্গ বাহিনী, ভারতীয় মজদুর সংঘ বা বি এম এস, নানা সাইজের সাধুদের হরেক রকম সংস্থা ইত্যাদি) এদের সহযোগী। কিন্তু এদের মধ্যে নানা বিরোধও মাঝেমাঝেই মাথা চাড়া দেয়। মহারাষ্ট্রে আমেরিকান সংস্থা এনরন প্রসঙ্গে শিবসেনা ও বিজেপির মতবিরোধ। আপাত ও সাময়িক হলেও গোপন নেই। গুজরাতে বিজেপি নেতৃত্বের ক্ষমতার লড়াই নগ্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তাদের মেয়েরাও গোলওয়ালকরের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীকে অস্বীকার করতে চাইছেন। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাদের দাবী ‘নারীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য নারীর আর্থিক স্বাধীনতা অত্যাবশ্যক। সুতরাং এই আর্থিক স্বাধীনতার প্রয়াসে চাকুরিরত মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ প্রয়োজন এবং এ সম্পর্কিত মামলার নিম্পত্তির জন্য মহিলা বিচারক আবশ্যক।’ (রাষ্ট্র সেবিকা। সমিতির পত্রিকা ‘জাগৃতি-তে প্রকাশিত; এখানে ‘খাকি প্যান্ট গেরুয়া ঝাণ্ডা’ থেকে সংগৃহীত) ভারতের চার পীঠের শঙ্করাচার্যদের সঙ্গে বজরঙ্গ দল বা বিশ্ব হিন্দুপরিষদ ইত্যাদির মতানৈক্য অজানা নয়। মুসলিম মৌলবাদীদের অসংখ্য সংগঠন রয়েছে। এবং ধর্মরক্ষার প্রশ্নে কে সাচ্চা তা নিয়ে বিরোধও আছে। সব মিলিয়ে অন্তত একই ধর্মের মৌলবাদীরা এক কাট্টা হয়ে, অতি সুসংহত ভাবে ভিন্ন ধর্মকে আক্রমণ করছে বা সমগ্ৰ দেশকে গ্ৰাস করতে চাইছে-এমন ভাবে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সমাজ ও সভ্যতার বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের পশ্চাদপদ মানসিকতাই শুধু তাদের প্রধান দুর্বলতা নয়, তাদের নিজেদের মধ্যে অনৈক্যও যে আছে সেটিও জেনে রাখা ভাল।
কিন্তু বহুশত বছরের অভ্যস্ত ব্যাপক ধর্মবিশ্বাসের কারণে তাদের যে সার্বিক ঐক্য রয়েছে তাকে উপেক্ষা করার কোন কারণ নেই, বিশেষত নবীন ও তুলনায় অনভিজ্ঞ বামপন্থার সাম্প্রতিক অনৈক্য ও দিশেহারা অবস্থার কথা মাথায় রাখলে। তাই বিশেষ ধর্মের প্রসঙ্গে একই ধর্মের কিন্তু বিচ্ছিন্ন সব মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলিই বিশেষ অবস্থায় অনৈক্য ভুলে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ক্ষমতা রাখে। আন্তর্জাতিকভাবে যেমন হয়েছিল ইসলামী মৌলবাদীদের ক্ষেত্রে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার পরে।
এখনকার বিশেষ বিশেষ ধর্মের মৌলবাদীরা নিজ নিজ এলাকায় ক্ষমতা দখলের লড়াই চালাচ্ছে। ভিন্ন ধর্মের মৌলবাদীরা এই এলাকায় যতক্ষণ না অনুপ্রবেশ করে, ততক্ষণ ভিন্ন ধর্মের হলেও, এইসব মৌলবাদীদের মধ্যেও ঐক্য রয়েছে—এই ঐক্যের ভিত্তি ধৰ্মরক্ষার তাড়না; হিন্দু হোক, ইসলাম হোক বা খৃস্ট হোক, সাধারণভাবে ধর্মের উপর আঘাত রুখতে তারা এক কাট্টা!! তাই বির্বতনবাদ বা মার্কসীয় দর্শনের উপর এরা সবাই খাপ্পা। পাকিস্থানে বা বাংলাদেশে মুসলিম মৌলবাদীরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করলেও কিংবা ভারতের বুকে বসে হিন্দু মৌলবাদীরা মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা বল্লেও মূলগতভাবে হিন্দু-মুসলিম মৌলবাদীরা ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা পরস্পরের শুভাকাঙ্খী ও সুহৃদ।
তাই দেখা যায় ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাজনের কিছু আগে জামাতে ইসলামী প্রকাশিত পুস্তিকায় (জামাতে ইসলাম কি দাওয়াৎ’) মওদুদীর বন্ধুত্বপূর্ণ আবেদন, ‘ভারতের একটি অংশ দেওয়া হবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠদের এবং অন্য একটি অংশ নিয়ন্ত্রিত হবে অমুসলমানদের দ্বারা। প্রথম অংশে (পাকিস্থানে)। আমরা জনমত সংগঠিত করবো যাতে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র ইসলামী আইনের উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়। অন্য অংশে আমরা হব সংখ্যালঘু এবং আপনারা (হিন্দুরা) হবেন সংখ্যাগুরু। আমরা আপনাদের অনুরোধ করব রামচন্দ্ৰ, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, গুরু নানক ও অন্যান্য সাধুসন্তদের জীবন ও শিক্ষা অধ্যয়ন করতে। দয়া করে বেদ, পুরাণ, শাস্ত্র ও অন্যান্য বই পাঠ করুন। এইসব থেকে যদি আপনারা কোন ঐশ্বরিক দিগনির্দেশ পান তাহলে তার ভিত্তিতেই আপনারা নিজেদের শাসনতন্ত্র তৈরী করুন। আপনাদের ধর্মের নীতি অনুযায়ী আপনারা আমাদের সঙ্গে আচরণ করুন। এ অনুরোধ আপনাদের করবো এবং এ নিয়ে আমরা কোন আপত্তি করব না।’ ১৯৫৩-তে দাঙ্গা শুরু করে এবং বহু কাদিয়ানীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। দাঙ্গার পর পাকিস্থান সরকার যে তদন্ত কমিশন করে তাতে সাক্ষ্য দিতে গিয়েও মওদুদী জানিয়েছিলেন, ‘ভারতের মুসলমানরা ঐ ধরনের সরকারে যদি ম্লেচ্ছ ও শূদ্র হিসেবেও বিবেচিত হয় ও সেখানে মনুর আইন জারি হয় এবং তারা সরকারে অংশগ্রহণের ও নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলেও আমি তাতে আপত্তি করব না।’
এটি অন্তত কিছুটা সুখের ব্যাপার ছিল যে, ১৯৪৭-এর পরে ভারত ধর্মীয় (হিন্দু) রাষ্ট্র হয় নি। কিন্তু এখনকার হিন্দু মৌলবাদীরা হিন্দুরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে খোয়াব দেখছে, তাতে মুসলমানদের প্রতি এদের বৈরি আচরণকেও যে মুসলিম মৌলবাদীরা সমর্থন করবে তাতে মনে হয় কোন সন্দেহ নেই। অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাসী জনগণের সঙ্গে নয়, মৌলবাদীরা একাত্ম মৌলবাদীদের সঙ্গেই। তাই দেখা যায়, ১৯৯২-এর ডিসেম্বরে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার অব্যবহিত আগে বাংলাদেশের জামাতেইসলামীর প্রতিনিধিরা অর্থাৎ মুসলিম মৌলবাদীরা, দিল্লিতে হিন্দু মৌলবাদীদের রাজনৈতিক মুখপাত্র ভারতীয় জনতাপার্টির নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক করে গেছে এবং ভ্রাতৃত্বমূলক সম্পর্ক দৃঢ়তর করে এসেছে। আসলে বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার কাজটি হিন্দু ও মুসলিম উভয় মৌলবাদীরই আকাঙ্খিত ছিল। হিন্দু মৌলবাদীরা এর ফলে হিন্দুদের সংগঠিত করতে পেরেছে; মুসলিম মৌলবাদীরা হিন্দুত্বের বা হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের খেপিয়ে নিজেদের সাংগঠনিক ক্ষমতা বাড়াতে পেরেছে। ধর্ম নির্বিশেষে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য বা তাঁদের বেঁচে থাকার লড়াইকে শক্তিশালী করার জন্য নয়, ধর্মের মত একটি কৃত্রিম পরিচয়কে কাজে লাগিয়ে এবং ধর্মবিশ্বাসকে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের স্তর থেকে নামিয়ে রাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্রে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে সব ধরনের মৌলবাদীরাই কাজ করে। এইভাবে সমস্ত ধর্মীয় মৌলবাদীদের চরিত্রই হচ্ছে জনবিরোধী,–এমন কি তারা নিজ ধর্মের জনসাধারণেরও স্বাৰ্থ দেখায় ততটা উৎসুক নয়, যতটা উৎসুক ধর্মকে রক্ষা করার অজুহাত সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে ক্ষমতা অর্জন করার জন্য তথা শাসক ও শোষক হিসেবে আপন শ্রেণীস্বার্থকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য। মুসলিম মৌলবাদীরা হিন্দু রাষ্ট্রে সাধারণ মুসলিমদের নাগরিক অধিকার না থাকলেও তেমন দুঃখিত হবে না। তেমনি হিন্দু মৌলবাদীরাও জন্মসূত্রে হিন্দু, এমনকি হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী। কিন্তু পরমতসহিষ্ণু, উদারনৈতিক ব্যক্তিদেরও ‘মেকি ধর্ম-নিরপেক্ষ বা ‘মুসলিম তোষণকারী’ হিসেবে ছাপ মেরে অনায়াসে শত্রুর পর্যায়ে ফেলে দিচ্ছে। তাই প্রকৃত অর্থে ধর্ম ও জনসাধারণের চেয়ে নিজেদের রাজনৈতিক ধান্দাবাজি ও শ্রেণী:স্বার্থটিই তাদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকার ফান্ডামেন্টালিস্টরাও অন্যান্য খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করেছে। মৌলবাদীরা একসময় এমন সংকীর্ণতায় আচ্ছন্ন হলেও ধর্ম তাদের কাজের একটি প্রাথমিক ভিত্তি। ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির সমগ্ৰতা জুড়ে ধর্মবিশ্বাস ছড়িয়ে থাকে। তার কাছে ধর্মের স্থান এবং মানুষের স্থান নিজের স্বার্থের উপরে। ধর্মীয় মৌলবাদীরা ধর্মের ছাঁই গায়ে মাখে, তার আড়ালে লুকিয়ে রাখে। নিজের শ্রেণীস্বার্থ ও প্রকৃত ধান্দাগুলিকে। মানুষকে প্রতারণা করার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এখনকার ধর্মীয় মৌলবাদীদের একটি উল্লেখযোগ্য দিক।
শ্ৰেণীবিভাজিত সমাজে সুবিধাভোগী শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণে যে রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালিত হয়, ঐ ব্যবস্থায় ধর্মীয় মৌলবাদীরা স্বাভাবিকভাবেই তাদের উর্বর বিচরণক্ষেত্র খুঁজে পায়। এই ধরনের রাষ্ট্র নিজ স্বার্থে ধর্ম ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা সহ সমস্ত ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল ও পশ্চাদপদ। চিস্তাকে সযত্নে লালিত করে। এমন কি কোন রাষ্ট্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে অগ্রসর’ হলেও তার অনুরূপ মানসিকতার গরিষ্ঠ সংখ্যক জনগোষ্ঠীর দ্বারা নির্বাচিত প্ৰতিনিধির মাধ্যমে সে এমনকি মৌলবাদকেও উৎসাহিত করে যায়।
তাই দেখা যায় আমেরিকার ফান্ডামেন্টালিস্টদের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় প্রধানদের গভীর বন্ধুত্ব একটি স্বাভাবিক ব্যাপার হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এ ব্যাপারে পূর্বোক্ত বিলি গ্রাহাম (Billy Graham; জন্ম ১৯১৮)-এর কথা বলা যেতে পারে। ১৯৫০এর মধ্যে ইনি ফান্ডামেন্টালিস্টদের প্রধান মুখপাত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯৪৯এ-আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হ্যাঁরি এস. ট্রম্যান একে হোয়াইট হাউসে প্রথম আমন্ত্রণ করে নিয়ে আসেন। এবং সেই শুরু। হোয়াইট হাউসে। তঁর যাতায়াত এর পর অতি নিয়মিতই ঘটতে থাকে। বিলি গ্রাহাম পরবর্তী প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার, জনসন ও নিক্সনের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও গলফ খেলার সঙ্গী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। রেগনের স্ত্রীর মত আমেরিকার ফাস্ট লেডিসহ বহু উচ্চশ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তিই জ্যোতিষীরও শরণাপন্ন হতেন বা হন। ফ্রান্সে রেজিস্টর্ড জ্যোতিষীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ইংল্যান্ডে রাজা বা রানী গীজাঁর অধিকর্তা এবং রাষ্ট্র থেকেই গীর্জার খরচ মেটানো হয়। আমেরিকার ধর্মীয় দক্ষিণপন্থীরা (religious rights) প্ৰবল ক্ষমতার অধিকারী এবং আগের নির্বাচনে রিপাবলিকান সাফল্যের পেছনে ‘বাইবেল বেল্ট (ফান্ডামেন্টালিস্ট)-দের ভূমিকা কম ছিল না। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট এদের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হন।
আর ভারতের মত দেশে তো কথাই নেই। বামপন্থী-দক্ষিণপন্থী সবাই জাতপাত ধর্মের রাজনীতি করে। তারা জনগণের মধ্যেকার এমন অমানবিক ও কৃত্রিম বিভাজনকে ব্যবহার করে নির্বাচনী কৌশল স্থির করে এবং এইভাবে এমন বিভাজনকে শক্তিশালী করে। আর্থিক প্রয়োজন নয়, জাত-পাতিভিত্তিক এই বিভাজন অনুযায়ী তারা শিক্ষা ও চাকরী সংরক্ষণ থেকে ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়া-নানাবিধ সুবিধা দিয়ে মানুষকে ভোলানোর চেষ্টা করে। বাম-ডান উভয় রাজনৈতিক নেতাই এটা ভুলে যান যে বা ভুলে থাকার ভান করেন যে, তথাকথিত মুচি, তাঁতী, চামার কিংবা সাঁওতাল-মুন্ড ইত্যাদি ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়-এর মধ্যেও শ্রেণীবিভাজন রয়েছে এবং ঐ সব অনুন্নত গোষ্ঠীর বেশির ভাগ মানুষই নিজেদেরই গোষ্ঠীর মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী মানুষের দ্বারাও শোষিত হন। এদের সবাইকে একই চোখে দেখে ঢালাও সুযোগ সুবিধা দেওয়ার মধ্যে তাদের নিজেদের মধ্যেকার শ্রেণীবিভাজনকে যেমন অস্বীকার করা হয়, তেমনি ঐ মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগীদের হাতই বেশি শক্ত করা হয়; আর মূল সমাজ থেকে তাদের চিহ্নিত করা ও বিচ্ছিন্ন করা তো হয়ই। পাশাপাশি তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষের দরিদ্রতম অংশকেও বঞ্চিত করা হয়। এই ধরনের জাত-পাতি-ধর্ম ভিত্তিক, তথাকথিত জনদরদী সংরক্ষণ-নীতির পাশাপাশি ভারতের মত দেশের রাষ্ট্রপতি-প্রধানমন্ত্রী-মন্ত্রীরা চন্দ্ৰস্বামী বা সাইবাবার মত গুরুদের তথা ধান্দাবাজ ধৰ্মজীবীদের পেছনে ঘুরঘুর করেন, মসজিদ-গীর্জামন্দিরে ভক্তির প্রদর্শন করেন, জ্যোতিষীদের অবাধ পরামর্শ গ্রহণ করেন। এঁদের এই সব কান্ড করার পেছনে একটি বড় যে মানসিকতা কাজ করে, তা হয়তো ভোলতেয়ার-এরও ছিল এবং তাই তিনি বলেছিলেন–
‘আমি চাই যে আমার চাকর-বাকরেরা ধর্মে বিশ্বাস করুক, তাহলে আমি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারব।’
ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক তোকভিল মন্তব্য করেছিলেন, ‘ফরাসী বিপ্লবের আগে দেশের অভিজাতশ্রেণী খুবই ধর্মবিরোধী ছিল। বিপ্লবের পর বিপদ বুঝে তারা আবার ধর্মের দিকে মুখ ফেরায়। তারপর এল। বুর্জেয়াদের পালা। তারাও বিপদ দেখে ধর্মের শরণ নিল।’
এই সব অভিজাত বা বুর্জোয়ারা যে সবসময় ধর্মীয় মৌলবাদী হবে তা অবশ্যই নয়। কিন্তু টুম্যান-আইনেহাওয়ার-জনসন-নিক্সনই হন বা ইন্দিরা-মুজিব-রাজীবনরসিমহা রাওরাই হন, —এঁরা প্রকাশ্যে ধর্মকে উৎসাহিত করতে, ধর্মের সুবিধাবাদী রাজনৈতিক ব্যবহার করতে এবং এমন কি নানা সময়ে ধর্মীয় মৌলবাদীদের সঙ্গী হতে পিছপা হন না। এই অবস্থায় ধর্মীয় মৌলবাদীরা উৎসাহ বোধ করে, শক্তি অর্জন করে এবং শত্রু হিসেবে ধর্মীয় মৌলবাদীদের চিহ্নিত করার ব্যাপারটি এর ফলে অনেক দুরূহ হয়ে ওঠে। অমৌলবাদী, গণতান্ত্রিক ও উদারপন্থী হিসেবে চিহিন্ত ঐ সব ব্যক্তিদেরই এক ধরনের সঙ্গী হিসেবে মৌলবাদীরা প্রতিষ্ঠিত হয়, হয়তো বা তাদের কাজটিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।
এই রাষ্ট্রব্যবস্থায় লালিত ধর্মীয় মৌলবাদের যথাসম্ভব সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক বৈশিষ্ট্য হল শ্রেণী-সমন্বয়ের মানসিকতা। বাস্তব অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাজনকে অস্বীকার করে, অলীক ও কৃত্রিম ধর্মীয় বিভাজন তথা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে ভিত্তি করেই তার সৃষ্টি ও টিকে থাকা। মার্কসীয় দর্শনকে সামনে রেখে যে সব রাজনৈতিক গোষ্ঠীর মধ্যে মৌলবাদী সংকীর্ণতা ও অসহিষ্ণুতা থাকে, তাদের সঙ্গে এটি একটি গুণগত বড় তফাৎ—এঁরা অন্তত মুখে শ্রেণীসংগ্রামের কথা বলেন। কিন্তু ধর্মীয় মৌলবাদীদের কাছে এই শ্রেণীবিভাজনই মূল্যহীন। হিন্দু, ইসলাম বা খৃস্ট-যে ধর্মেরই হোক না কেন ঐ ধর্মাবলম্বী সবার স্বার্থ যে এক নয় তা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ অস্বীকার করে। একই ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে শাসকশাসিত বিভাজন আছে। হিন্দু শাসক ও শোষক হিন্দুদের মৃদুভাবে শাসন করে ও কম শোষণ করে তা নয়। হিন্দু জমিদার হিন্দুপ্রজাদের উপর অত্যাচার করে না তা-ও নয়। হিন্দু পুঁজিবাদীরা হিন্দু জনসাধারণের কাছে থেকে কম মুনাফার চেষ্টা করে সেটিও নয়। এবং ব্যাপারটি সব ধর্মের ক্ষেত্রেই সত্য। পাকিস্থান বা বাংলাদেশের মত যে সব দেশে ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম, নেপালের মত যে দেশ সরকারী ভাবে হিন্দু রাষ্ট্র, বলিভিয়া-আর্জেন্টিনা-অ্যান্ডোরার যে সব দেশ সরকারীভাবে খৃস্টধর্মাবলম্বী—সেই সব দেশে অন্তত একই ধর্মের সব মানুষ আর্থিক ও সামাজিকভাবে সমানাধিকার ভোগ করে, ধনী-দরিদ্র বিভাজন নেই, বিপুল সংখ্যক মানুষ নিকৃষ্ট জীবন যাপন করে না-তা আদৌ নয়। বিশেষ ধর্মকে বিশেষ দেশের রাষ্ট্ৰীয় ধর্ম করলেই আর যাই হোক বিপুল সংখ্যক মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধান আদৌ হয়নি, হবেও না। বরং তার জন্য মানুষের বেঁচে থাকার যে আন্দোলন তা বিপথগামী ও বিলম্বিত হবে। কারণ ধর্ম ও ধর্মীয় মৌলবাদ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় বিভেদকেই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিভেদ বলে গ্রহণ করতে শেখায়। এর ফলে এক হতদরিদ্র হিন্দু বা মুসলিম কৃষক কিংবা বেকার ও হতাশ এক তরুণ ভিন্ন ধর্মের মানুষকে, যে হয়তো তারই মত দরিদ্র ও হতাশাগ্ৰস্ত, তাকে শত্রু বলে ভাবতে থাকে-আর আড়ালে থেকে নিশ্চিন্ত উল্লাসে ঠাকরে-আদবানি-ঋতম্ভরামওদুদী-গোলাম আজমরা পরস্পরের পিঠে সুড়সুড়ি দেয়।
ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্মীয় মৌলবাদীরা এইভাবে শোষিত শ্রেণীর মধ্যকারী সংগ্ৰামী ঐক্যকে ও ঐক্যের সম্ভাবনাকে ভেঙ্গে চুরমার করতে থাকে। ধৰ্মীয় রাষ্ট্রের শাসককুল এই উদ্দেশ্যেই বহু লড়াই’ (অর্থাৎ ধান্দাবাজি) করে দেশকে ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে তোলে। এবং সবচেয়ে করুণ, নির্মম দিক হল তাদের এই লড়াইতে তারা গাধার সামনে গাজর ঝোলানোর মত শোষিত মানুষের সামনের ধর্মের গাজর ঝুলিয়ে রেখে ধর্মবিশ্বাসী বা ধর্মের প্রতি মোহগ্ৰস্ত অজস্ৰ সাধারণ মানুষকেও সহযোদ্ধা’ হিসেবে জোগাড় করে নেয়। এই ‘যোদ্ধারা’ধর্মকে রক্ষণ করার মহান ব্রত পালন করছে ভেবে শহিদ হতেও পিছপা হয় না। (এই ভাবেই তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়)। আসলে তারা শহিদ হয়, তাদেরই সিংহাসনে বসানোর জন্য যারা ভবিষ্যতে তাদেরই শাসন ও শোষণ করবে।
এই সিংহাসনে বসতে ইচ্ছুক ব্যক্তিরা যে আলাদা একটি শ্রেণী আর যাদের ঘাড়ে পা দিয়ে তারা এই লক্ষ্য পূরণ করতে চাইছে তারা যে ভিন্ন আরেকটি শ্রেণী, ধর্মীয় মৌলবাদী আন্দোলন এই সত্যটিকে ভুলিয়ে দেয়। নিছক একই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্যই শোষিত মানুষেরা শাসকশ্রেণীকে নিজেদের মিত্র বলে ভাবতে শেখে। এটি ঠিকই যে আদর্শ শ্রেণীবিভাজন। এখন আর নেই এবং শাসকশোষিত বিভাজন এখন অনেক জটিল। এই বিভাজন অনেক ক্ষেত্রেই আপেক্ষিক এবং শাসক শ্রেণীর নিম্নস্তরের সদস্যরা উচ্চ অবস্থানের শাসকদের দ্বারা শাসিত ও শোষিত হয়। তাই শাসক-শাসিত বা শোষক-শোষিতের বিভিন্ন স্তরবিন্যাস রয়েছে। ধর্মীয় মৌলবাদ এ ধরনের স্তরবিভাজনকেও অস্বীকার করে এবং তাদের লক্ষ্য থাকে। এ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন না হতে দেওয়া। তাই দেখা যায়,–
‘আর এস এস-কর্মীদের ছোটোবেলা থেকেই শিক্ষা দেওয়া হয় যুক্তিতর্কের ধার না ধারতে এবং হিন্দুসমন্বিত সমাজ সম্পর্কে তাদের যে ধারণা গড়ে তোলা হয় তাতে স্পষ্টতই সমাজে শ্রেণী, জাতপাত এবং পুরুষ-নারী বিরোধ–এসব এড়িয়ে যায় এবং পুরোপুরি পুরুষ শাসিত, উচ্চবর্ণের এবং মধ্য এবং নিম্নমধ্য শ্রেণীর সদস্যদের নিয়ে গঠিত সমাজের ধারণার সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়।’ (খাকি প্যান্ট, গেরুয়া ঝান্ডা)
এবং ব্যাপারটি অন্যান্যদের ক্ষেত্ৰেও সত্য। আমেরিকার ফান্ডামেন্টালিস্টরা প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছিল বিবর্তনবাদ, কম্যুনিজম, বাইবেলের সমালোচনা, ইত্যাদিকে, কিন্তু কোন বিশেষ শ্রেণীকে নয়। বরং তারা উপযুক্ত পরামর্শ দিয়ে (কম্যুনিজমবিরোধী বৈদেশিক নীতি, সামরিক খাতে ব্যয় বাড়ানো ইত্যাদি ইত্যাদি) শাসকশ্রেণীর হাত শক্ত করতেই চেয়েছিল এবং এখনো চায়। পাকিস্থান-এ বাংলাদেশের মুসলিম মৌলবাদীদের প্রতিনিধি ঐ জামাতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মওদুদীও পাকিস্থানে ও ভারতে যথাক্রমে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের উপর ভিত্তি করে শাসনতন্ত্র গড়ে তোলার প্রেসক্রিপশান করেছেন, কোন জনস্বার্থবাহী জনগণতান্ত্রিক নীতির উপর ভিত্তি করে নয়। এবং তিনি আরো স্পষ্টভাবে শ্রেণীবৈষম্যকে অস্বীকার করে পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের, জমিদার ও কৃষকদের, শাসক ও শাসিতকে একাকার করে দিয়েছেন (‘…in an Islamic country there is no conflict between capitalist and workers, landlords and peasants, rulers and the ruled.’) মওদুদীর বদলে ঠাকরে-আদবানিদের বসালে এবং ইসলামিক দেশের বদলে হিন্দু রাষ্ট্রের কথা বল্লেও ভাষা ও ভাব হুবহু একই।
ধর্মীয় মৌলবাদের এই শ্রেণী সমন্বয় বা শ্রেণী বিভাজনকে অস্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ তাদের নারীবিদ্বেষী চরিত্র। ধর্মীয় মৌলবাদ মূলগতভাবে পুরুষতান্ত্রিক। নারী-পুরুষের সামাজিক অর্থনৈতিক বৈষম্যকেও সে অস্বীকার করে। নারী তার কাছে অনুগত একটি বিশেষ গোষ্ঠী মাত্র। ধর্ম এবং ধর্মীয় মৌলবাদের মায়ায় আচ্ছন্ন নারীরাও এই নারীবিদ্বেষী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের শিকার। যেভাবে আজীবন অবহেলিত এক শাশুড়ি সুযোগ পেয়ে পুত্রবধুর উপর অত্যাচার চালায়, তেমনি ধর্মমোহে আচ্ছন্ন এই সব নারীরাও তাদের-অপমানিত-অবদমিত সামাজিক অবস্থানের মধ্যে, আপাত তৎপরতার বা কর্তৃত্বের আস্বাদ পেয়ে নারীসমাজকে নিষ্পেষিত করতে পুরুষ শাসিত মৌলবাদকে সাহায্য করে যায়। হিন্দু মৌলবাদের উস্কানিতে তারা বাবরি মসজিদ ভাঙ্গতে দলে দলে এগিয়ে যায়, মুসলিম মৌলবাদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে তারা বোরখার স্বপক্ষে ও শরীয়তী আইনের স্বার্থে মিছিল বের করে। এমন নারীর সংখ্যা তুলনায় সীমিত হলেও, তাদের সংখ্যা একেবারে কম নয়। যে কৌশলে ধর্মীয় মৌলবাদ সরল ধর্মবিশ্বাসী জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাদের প্রতারণা করে এবং নেতৃত্বের শ্রেণীস্বর্ধকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, ঐ একই নির্মম কৌশলে তারা ধর্মবিশ্বাসী নারীদেরও ব্যবহার করে। বেদ বাইবেল কোরান মনুসংহিতা হাদিস বা অর্থশাস্ত্রের ছত্ৰে ছত্ৰে নারী অবদমনের কথাবার্তা ছড়িয়ে রয়েছে। কোরানে নারীর সম্পত্তির অধিকার জাতীয় কিছু কিছু মানবিক নির্দেশ থাকলেও নারীর স্থান যে পুরুষের নীচে, অবাধ্য নারীকে যে গৃহে আবদ্ধ করে রাখা যায় ইত্যাদি ধরনের কথাও দ্বিধাহীনভাবে বলা হয়েছে। ইসলামী আইনে ব্যভিচারে অভিযুক্ত নারীকেই নিজের নির্দোষিতার প্রমাণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। নারীর সাক্ষ্যের মূল্য যে পুরুষের সাক্ষ্যের চেয়ে অনেক কম তাও বলা হয়েছে দ্বিধাহীনভাবে। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থে (শীতপথ ব্রাহ্মাণে) ‘কুকুর ও শূদ্রের’ মত নারীরাও যে ‘অসত্য, পাপ ও অন্ধকার’ তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং এ ধরনের উদাহরণ অসংখ্য। আর এসব বক্তব্যের মর্মবস্তু যে পুরুষশাসিত সমাজ, তাকে গ্ৰহণ করেই ধর্মীয় মৌলবাদের চরিত্র পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।
কিন্তু ধর্মবিশ্বাসী নেতৃত্ব মাত্রেই এমন নারীবিদ্বেষী তা নন। তাই দেখা যায় সম্রাট আকবর মুসলমানদের যথেচ্ছ তালাক করার প্রথা রদ করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। মুসলিমদের একটি গোষ্ঠী মুতাজিলাহ-রা বা ঈশ্বরবিশ্বাসী ধর্মপ্রাণ মহাত্মা গান্ধী নারীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং এমন ধর্মনিষ্ঠ কিন্তু নারীদের প্রতি সম্মান ও সহানুভূতি প্রদর্শন করার মানুষ অসংখ্যই আছেন। কিন্তু ধর্মীয় মৌলবাদীরা এঁদের থেকে পৃথক। মৌলবাদীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ধর্মের মূল দৃষ্টিভঙ্গীগুলিকে ঈশ্বরদত্ত বলে প্রচার করা ও অন্ধভাবে আঁকড়ে রাখা। এরই একটি অংশ এই নারীস্বার্থবিরোধী পুরুষতান্ত্রিকতা তথা পুরুষ আধিপত্য। নারীপুরুষের সার্বিক সমানাধিকার ও সহযোগিতা তাদের ভাব ও ভাবনা থেকে বহু দূরে। এক্ষত্রে হিটলার তথা ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে তাদের দৃষ্টিভঙ্গীগত মিলের কথা আগেই বলা হয়েছে।
ইরান-পাকিস্তান-আলজিরিয়া সর্বত্র এই মৌলবাদীরা মেয়েদের উপর বোেরখা চাপিয়ে চাকরি থেকে দূর করে দিতে চাইছে। এরা মুসলিম ধর্মের জোব্বা গায়ে চাপায়। হিন্দুত্বের নামাবলী গায়ে জড়িয়ে ভারতেও হিন্দু মৌলবাদীরা একই কথা বলে। তাদের নারীবিভাগ রাষ্ট্র সেবিকা সমিতিও এই ফাঁদে পা দিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন মূল্য নেই,—পারিবারিক সিদ্ধান্তই বিবাহ, পেশা ও কর্মক্ষেত্রের বিষয়ে চূড়ান্ত এবং এমনকি সংগঠনে কাজ করার ব্যাপারটিও। সানন্দে উদাহরণ দেওয়া হয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কমী-সমর্থক এক মহিলার, যিনি সস্তানের দেখাশুনা করার জন্য ব্যাংকের বড়ো চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন। পারিবারিক স্বাৰ্থ, সন্তানের যত্ন, যৌথ সিদ্ধান্ত ইত্যাদি অবশ্যই গুরুত্বহীন নয়, কিন্তু যখন তা নারীর আপন ব্যক্তিত্ব যোগ্যতা ও স্বাধীন ইচ্ছাকে আদৌ মূল্য দেয় না। তখন সেটি আর যাই হোক নারীস্বার্থবাহী থাকে না। এবং তা নারীর স্বাৰ্থ যদি না দেখে, তবে সেটি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপর পক্ষের অর্থাৎ পুরুষের স্বাের্থই দেখে। হিন্দু মৌলবাদীরা সম্প্রতি অবশ্য দরিদ্র-বেকার যুবক কিশোর, শ্রমিক কৃষকদের মত মেয়েদেরও দাবার বোড়ে হিসেবে ব্যবহার করছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী সুন্দরভাবে বৈষম্যমুক্ত।
রাজনৈতিক জ্ঞান-ও ব্যক্তিত্ব-হীন কিন্তু সুন্দরী চিত্ৰতারকা বা দূরদর্শন তারকাকে (হায় সীতা!) তারা নিছক তার গ্ল্যামার ও শারীরিক সৌন্দর্যের কারণে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে নামিয়ে দিয়েছে। এখানেও নারীর বাহ্যিক সৌন্দর্য ও অভিনেত্রী হিসেবে আনন্দদায়িনী ভূমিকাই বড় করে ধরা হয়। (তবে ব্যাপারটি শুধু মৌলবাদীদের ক্ষেত্রে নয়, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস থেকে তেলেগু দেশম,–নানা রাজনৈতিক দলগুলির ক্ষেত্রেও সত্য। মৌলবাদীদের মত এক্ষেত্রে এদেরও উদ্দেশ্য থাকে, চটক ও সস্তা জনপ্রিয়তাকে মূলধন করে কোনভাবে গর্দিটা লাভ করা। আদর্শবোধ বা রাজনৈতিক চেতনা ইত্যাদি। এদের সবার কাছেই গৌণ একটি ব্যাপার।)
অন্যদিকে হাজার হাজার কিশোরী-যুবতী-প্রৌঢ়ারা করসেবিকা নাম দিয়ে গডডলিকা স্রোতে এগিয়ে যায় অযোধ্যার সত্যগ্রহে বা বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার উন্মাদনায়। ঝামেলার মুখে বা মিছিলের সামনে মেয়েদের লেলিয়ে দেওয়ার এ আরেকটি চিরাচরিত পৌরুষী ও নোংরা কৌশল। যদিও ঋতম্ভরা তাঁর বক্তৃতায় বোনেদের নয়, ভাইদের জাগার কথা বলেছিলেন (‘বীর ভাইয়ো জাগো’), তবু তিনি সহ আরো বহু মহিলারাই জগতে শুরু করেছেন। কিন্তু এই নারী জাগরণ নিজেদের সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতা নয়, বরং তা ভুলিয়ে দেওয়ারই একটি উপায় মাত্র। তাই হিন্দুধর্মের তথা ধর্মের পিতৃতান্ত্রিকতার কোন সমালোচনামূলক কথাবার্তা তাদের মাথাতেও আসে না। গোলওয়ালকারের নারীস্বার্থবিরোধী সংকীর্ণতাকে অস্বীকার করে, হিন্দু মৌলবাদের খপ্পরে থাকা নারীদেরও কেউ কেউ সম্প্রতি নারীর আর্থিক স্বাধীনতা’-র কথা বলছেন। কিন্তু এমন কথাবার্তা এত নীচ সুরে বাঁধা যে, ধৰ্মরক্ষার (অর্থাৎ নারীবিদ্বেষী পুরুষশাসিত সমাজের স্বৰ্থবাহী বিশেষ প্রতিষ্ঠানিক ধর্মকে রক্ষার) তীব্রতার কাছে তা মূল্যহীন হয়ে ওঠে।
মৌলবাদের এ জাতীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হলেও, এটিও সত্য যে অমৌলবাদী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগুলি যে এ ধরনের সমস্ত বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত তা নয়। মৌলবাদী না হওয়া মানেই শ্রেণী সচেতন, জনস্বার্থবাহী, শাসক শ্রেণীবিরোধী ও শ্রেণী সংগ্রামের অন্যতম যোদ্ধা হয়ে ওঠা তাও নয়। ধর্মীয় মৌলবাদী বা সাম্প্রদায়িক না হওয়ার অর্থ কম্যুনিস্ট হয়ে যাওয়া বা বস্তুবাদী দর্শনের ছাত্র হয়ে যাওয়া-সেটিও আদৌ নয়। এটি অতি সুস্পষ্ট একটি সত্য। মহাত্মা গান্ধীও কম্যুনিজমবিরোধী ছিলেন, পুঁজিবাদের তথা পুঁজিপতিদের কোন ধরনের ক্ষতি হোক তা তারও কাম্য ছিল না, ঈশ্বর ও ধর্মে ছিল তার অচলা আনুগত্য ইত্যাদি। কিন্তু তাকে ধর্মীয় মৌলবাদী বা সাম্প্রদায়িক বলা যায় না। বড়জোর এটি বলা যায় যে, তার মানসিকতা ও কাজকর্ম ধর্মীয় মৌলবাদের সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম। এবং এ ধরনের ব্যক্তিত্বের উদাহরণ। অসংখ্য রয়েছে। সাধারণভাবে ধর্মবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রেও তা সত্য।
প্ৰতিষ্ঠানিক ধর্মের অস্তিত্ব ও এইসব ধর্মে বিশ্বাস না থাকলে ধর্মীয় মৌলবাদ (ও সাম্প্রদায়িকতার) সৃষ্টি হওয়ার ও টিকে থাকার সম্ভাবনাই থাকে না। তাই ধর্মবিশ্বাসীরা আসলে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাকে ফক্ষুধারার মত লালন করেন। বিশেষ সময়ে ও পরিস্থিতিতে এই ধারা কারোকারোর ক্ষেত্রে প্রকাশ্য হয়ে বন্যার আকার ধারণ করে। তবু তাদের বৃহদংশই প্রকাশ্যে ধর্মীয় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতাই করেন। এঁরা ধর্মের গ্রহণীয়, নমনীয়, সহনীয়, উদার রূপকে টিকিয়ে রাখতে আগ্রহী। কিন্তু ধর্মীয় মৌলবাদীরা ধর্মের অবৈজ্ঞানিক, প্রতিক্রিয়াশীল, শাসকশ্রেণীর স্বার্থবাহী, পুরুষ আধিপত্যকামী এবং ধর্মের নামে মানুষকে কৃত্রিমভাবে বিভক্ত করার জনস্বার্থবিরোধী দিকগুলিকে হিংস্র ও চরমভাবে তাদের কথায় ও কাজে প্রকাশ করতে চায়। জনসমর্থন আদায়ের জন্য তারা ধর্মবাদী জাতীয়তাবাদের প্রচার করে। তাদের সংকীর্ণ শ্রেণীস্বার্থ এসবের পেছনে ইন্ধন জুগিয়ে চলে।
————–
* ভারতীয় জনসঙ্ঘের লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা না করে শুধু তার সভাপতি বলরাজ মাধোককে উদ্ধৃত করা যায়।-’ভারত হিন্দুরাষ্ট্র হলে ইন্ডিয়া নাম মুছে ফেলা হবে। নাম হবে। হিন্দুস্তান। জাতীয় পশু হবে গরু। রাষ্ট্রভাষা হবে সংস্কৃত। যোগাযোগের ভাষা হবে হিন্দি-বলেছেন ভারতীয় জনসঙ্ঘের সভাপতি বলরাজ মাধোক। বুধবার। কলকাতায়।’ (আজিকাল; ২৫.৫.৮৯.)
** ভারতীয় জনতা পার্টির মত হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলি (যাদের সাধারণ ভাবে হিন্দু মৌলবাদী বলা যায় ও বলা হচ্ছে), তারা এই রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের শিক্ষা ও নীতিতেই প্রশিক্ষিত। বিজেপি (rIS 267 (5 Stifts (Tiri 4GIC2, ‘I am proud that my virtues have been imbibed from RSS,” (The Statesman; 17.995)
৪. মৌলবাদের জন্মকথা
মানবসভ্যতার ইতিহাসে ধর্মীয় মৌলবাদ অতি প্রাচীন যেমন কোন ব্যাপার নয়, তেমনি আচমকা সৃষ্টিও হয় নি। ধর্মকে অনাবিল ব্যক্তিগত বিশ্বাসের অবস্থান থেকে উৎখাত করে, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণী:স্বার্থে তার চরম ব্যবহার থেকে তার উদ্ভব। সাধারণভাবে বল্লে মৌলবাদের সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে হয়তো এভাবে প্রকাশ করা যায়।–
অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস
(এখন থেকে ৫০-৬০ হাজার বছর আগে নিয়ানডার্থাল মানুষের অন্তিম পর্যায়ে। এর থেকে ধীরে ধীরে ঈশ্বর ও আত্মার প্রাথমিক কল্পনার উন্মেষ। প্রধান ভূমিকা পালন করেছে—’মানুষের’ কল্পনা করার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার উন্নত ক্ষমতা, প্রকৃতির কাছে ও প্রকৃতি সম্পর্কে তার অসহায়তা ও অজ্ঞতা।)
↓
প্ৰতিষ্ঠানিক বিভিন্ন ধর্ম
(এখন থেকে প্রায় ৬ হাজার বছর আগে। প্রধান ভূমিকা পালন করেছে—শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সৃষ্টি; মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা তথা অনুশাসন সৃষ্টি করে গোষ্ঠীকে সুসংহত ও ঐক্যবদ্ধ রাখার তাগিদ)
↓
ধর্ম-নিষ্ঠা
(ঐশ্বরিক শক্তিকে সন্তুষ্ট রাখার বিশ্বাস ও তাকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিগত সততা–>এগুলি এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট)
↓
ধর্মান্ধতা বা ধর্মীয় গোঁড়ামি
(প্রধান ভূমিকা পালন করে বিশেষ শ্রেণীর উসকানি, চূড়ান্ত সংকীর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক মানসিকতা, নিজ ধর্মের বিরুদ্ধে ভিন্ন ধর্মের বা ভিন্নতর সামাজিক শক্তির আক্রমণ ও চ্যালেঞ্জের প্রতিক্রিয়া)
↓
ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা । ধর্মীয় পুনরভ্যুত্থানবাদ
↓
ধর্মীয় মৌলবাদ
(বিশুদ্ধ ধর্মীয় পুনরভ্যুত্থানবাদ নিজ ধর্মের তথাকথিত বিপন্ন অস্তিত্বের সময় তার মাহাত্ম্য ও কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চায়। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার প্রধান দিক হচ্ছে, মানুষের কৃত্রিম ধর্মীয় পরিচয়কেই প্রধানতম পরিচয় হিসেবে মনে করা, এইভাবে মানুষের মধ্যে বিভেদ ও শক্ৰতা সৃষ্টি করা, মানবিক সৌভ্রাতৃত্ব বিনষ্ট করা এবং নিজ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সমস্ত মানুষের স্বাৰ্থ এক বলে প্রচার করা ও ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষকে শত্রু বা অনুগত থাকার যোগ্য বলে মনে করা। ধর্মীয় মৌলবাদী ধর্মের সুবিধাজনক মূল ভিত্তিটিকে আপোষহীনভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং ধর্মান্ধিতা, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় পুনরভ্যুত্থানবাদের নানাদিক তার সঙ্গে সম্পৃক্তভাবে মিশে থাকে। ধৰ্মজীবী শাসক-শ্রেণীর বিপন্ন বা মুমূর্ষ। অবস্থায় অথবা শাসকশ্রেণীর একাংশের দ্বারা রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মের বীভৎস ব্যবহারের দ্বারা তার উদ্ভব।)
ধর্মীয় মৌলবাদ ও মৌলবাদী মানসিকতা এইভাবে বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে এক সময় সৃষ্টি হলেও তা আদৌ সর্বজনীন নয়। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসের ব্যাপারটিই একসময় সর্বজনীনতা লাভ করেছিল, যদিও এখন থেকে আনুমানিক আড়াই-তিন হাজার বছর আগে বস্তুবাদী চিস্তার উন্মেষের ধারাবাহিকতায় তা আজ আর সর্বজনীন নেই। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানিক বিভিন্ন ধর্ম থেকে ধর্মীয় মৌলবাদ সৃষ্টির প্রক্রিয়া অব্দি-সমস্ত স্তরেই আপামর জনসাধারণ তার অংশীভূত হয় নি। একসময় প্রতিষ্ঠানিক ধর্মগুলিতে বিশ্বাসীর সংখ্যা-তা যে যত আলগাভাবেই হোক না কেন, ছিল তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি। ঐ তুলনায় ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির সংখ্যা প্রকৃত বিচারে ছিল অনেক কম। আর ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় মৌলবাদীর সংখ্যা আরো কম। মানুষের চিরন্তন শুভবুদ্ধিরই একটি পরিচয় এটি-যদিও তাদের দ্বারা প্রভাবিত, বিপথগামী, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সংখ্যা অনেক।
ধর্মনিষ্ঠ বা ধর্মপ্ৰাণ (devoted to religion, virtuous, pious) ব্যক্তির সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। সুস্থ জীবনের লক্ষ্যে, নিজ ধর্মবিশ্বাসকে, তার আচার অনুষ্ঠান ও শিক্ষাকে নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে অনুসরণ করাই তাঁর জীবন-যাপনের প্রধান দিক। মৌলবাদীরা ধর্মনিষ্ঠ নয়; ধর্ম এদের কাছে নিষ্ঠার চেয়ে নিজের স্বাৰ্থ পুষ্ট করার, মানুষকে বিভক্ত করে তথা তার সামগ্রিক আন্দোলনে অনৈক্য সৃষ্টি করে হিংস্রতা প্রকাশ করার একটি মাধ্যম মাত্র। ধর্মীয় মৌলবাদী বলতে একদল এমন ‘মানুষ’কে বোঝায় যাদের মধ্যে ধর্মকে আঁকড়ে রেখে উগ্রতা ও হিংস্ৰতা (এই উগ্রতা ও হিংস্ৰতা সর্বদা নিছক শারীরিক নয়) ধর্মান্ধতা ও পরমত অসহিষ্ণুতা, প্রগতিবিরোধিতা ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদির ব্যাপারটি প্রধানভাবে চোখে পড়ে। এর বিপরীতে একজন ধর্মনিষ্ঠ মানুষের কথা বললে বা শুনলে চোখের সামনে প্রথমেই ভেসে আসে ধর্মে নিষ্ঠাবান, মানবপ্রেমিক, উদার একজন মানুষের মুখ। একদা যে অসম্পূর্ণ জ্ঞান ও অসহায়তা থেকে ঈশ্বর ও আত্মাসহ ধর্মের প্রাথমিক ভিত্তিগুলি কল্পিত হয়েছিল, তারই ধারাবাহিকতায় ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা ধর্মকে আঁকড়ে রাখেন নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পূক্তভাবে জড়িয়ে। তাকে শ্রেণীস্বার্থে ব্যবহার করা, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি বা রাজনৈতিক ধান্দাবাজির জন্য ব্যবহার করা থেকে অনেক দূরে তাঁর অবস্থান। ভিন্ন ধর্মের মানুষ তাঁর কাছে শত্রু নয়, তাকে তিনি র্তারই মত ধর্মনিষ্ঠ আরেকজন বলেই গণ্য করেন এবং সম্মান করেন।
ধর্ম যার প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেই রিলিজিয়ন (Religion) কথাটি এসেছে re-ligare থেকে যার আদি অর্থ হল ‘পুনর্বন্ধন’ (এই, ligare থেকেই এসেছে ligament কথাটি)। অর্থাৎ দুটি ভিন্ন মানুষকে যা বন্ধন করে তাই রিলিজিয়ন। সংস্কৃত তথা বাংলা ‘ধর্ম-এরও অর্থ যা ধারণ করে, মানুষকে ও মানুষের সমাজকে। ছিন্নবিচ্ছিন্ন শতধাবিভক্ত মানুষ নিয়ে সমাজ-ধারণ সম্ভব নয়। এইভাবে সমস্ত দিক বিচারে ধর্মের মূলগত অর্থেই ধর্মনিষ্ঠদের বিপরীতে ধর্মীয় মৌলবাদীরা ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা আদৌ ধাৰ্মিক নয়, বরং তারা ধর্মবিরোধী—যে ধর্ম মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা ও ধর্মীয় মৌলবাদীরা সেই ধর্মকে সামনে রেখেই ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের শত্রু বলে দূরে সরিয়ে দেয়। (অবশ্য পরবর্তীকালে ধর্ম বা রিলিজিয়নের এই মূলগত অৰ্থও হাস্যকর হয়ে গেছে, যখন থেকে বিশেষ প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম বিশেষ গোষ্ঠীর বা শ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে।)
এগুলি সত্ত্বেও এটিও সত্য যে, ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির মধ্যে নিজ ধর্মবিশ্বাসের প্রতি এক ধরনের অন্ধত্ব থাকে, যা ধর্মান্ধতা-ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা-ধর্মীয় মৌলবাদেরও একটি প্রাথমিক ভিত্তি। কিন্তু শেষোক্তারা যখন ধর্মবিরোধী বা ধর্মের ভিত্তিকে নাড়া দিতে সমর্থ প্রগতিশীল চিন্তাকে (যেমন বিবর্তনবাদ, বস্তুবাদ ইত্যাদি) হিংস্রভাবে মোকাবিলা করে, ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা তাকে উপেক্ষার চোখে দেখেন।
মৌলবাদীরা যখন ধর্মের মূল ভিত্তিতে ফিরে যাওয়ার জন্য জঙ্গী আন্দোলন ও প্রচার করে, ধর্মনিষ্ঠরা তখন নিজের জীবনে তার প্রয়োগ করেই তৃপ্ত থাকেন। সব মিলিয়ে ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কাছে ধর্ম নিজস্ব ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ব্যাপার। কিন্তু ধর্মীয় মৌলবাদী তথা সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিবর্গের কাছে তা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের একটি সাংগঠনিক মাধ্যম বা উপায় যা ধর্মের সঙ্গে ততটা যুক্ত নয়। এই উদ্দেশ্য নানা ধরনের হতে পারে,–(ক) নিছক ধর্মীয় মাহাত্ম্য বা বিপন্ন হওয়া ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য, এবং (খ) তার নাম করে নিজেদের শ্রেণীগত আধিপত্য বিস্তার করা ও ক্ষমতা অর্জন করা; এক্ষেত্রে অর্থনীতি ও রাজনীতির নানা দিক যুক্ত করা হয়। দ্বিতীয়োক্ত এই বিশেষ অধ্যমীয় উদ্দেশ্য না থাকার কারণে ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরা একক বা বিচ্ছিন্নভাবেই সাধারণতঃ থাকেন, কেউ বা হিমালয়ের নির্জনে ধ্যান আর ঈশ্বর আরাধনার কল্পিত আনন্দে নিমগ্ন থাকেন। অবশ্য যৌথভাবে ধর্মাচরণের জন্য কেউ বা হরিসভা জাতীয় নানা ধরনের ধর্মীয় ক্লাবও গড়েন। অন্যদিকে ধর্মের নাম করে বিশেষ কাৰ্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ধর্মীয় মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিরা সাধারণতঃ সংগঠিত হয়ে বিভিন্ন সংস্থা গড়ে তোলে, এমন কি এখনকার পরিবেশ পরিস্থিতি অনুযায়ী নানা ধরনের রাজনৈতিক দলও।
ধর্মীয় সংগঠনও নানা ধরনের হয়। নিছক সংগঠিত হলেই যে, তার মধ্যে মৌলবাদী বা সাম্প্রদায়িক ধান্দা থাকবে তা অবশ্যই নয়, যেমন পাড়ার কিছু ধর্মপ্ৰাণ ব্যক্তি ধর্মকে কেন্দ্র করে আনন্দলাভ করা ও অবসর বিনোদনের জন্য ঐ হরিসভা জাতীয় নানা সংস্থা গড়ে তুলতে পারেন। আবার সাইবাবা, অনুকূলচন্দ্ৰ, মোহনানন্দ, আনন্দময়ী মা, রজনীশ জাতীয় অজস্র গুরুমা-গুরুমহাশয়দের দল ব্যক্তিগত ব্যবসা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির জন্য ধর্মকে কাজে লাগিয়ে এবং সরলবিশ্বাসী মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে ধর্ষণ করে নিজেদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। কখনো বা লোকনাথ বা বালক ব্ৰহ্মচারীর মত লোকদের মৃত্যুর পরেও তার ধান্দাবাজ কিছু ‘ভক্ত’ ব্যবসায়িক কারণে এই ধরনের ব্যবসায়িক সংস্থা জিইয়ে রাখে। পাশাপাশি রামকৃষ্ণ মিশন জাতীয় ধর্মীয় সংস্থাও গড়ে ওঠে, যাদের প্রধান দিক নিজ ধর্মীয় মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি সমাজ সেবা, শিক্ষা প্রসার, কিছু বিশেষ মূল্যবোধ গড়ে তোলা ইত্যাদি।
এমন নানা ধরনের ধর্মীয় বা ধর্মভিত্তিক সংগঠনের পাশাপাশি ধর্মীয় মৌলবাদী বা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক সংগঠন আরো নিকৃষ্ট উপায়ে ধর্মকে কাজে লাগায়। এদের মধ্যে তীব্রতার তারতম্য থাকে। সব ধর্মেই মাহিষ্য সমিতি, বৈষ্ণব সম্মেলন, শৈব সভা বা সাদগোপ সভার মত নিছক সাম্প্রদায়িকতা ভিত্তিক নানা সংস্থা তৈরী হয়। বিশেষ ধর্মীয় গোষ্ঠীগত ও সাম্প্রদায়িক স্বাৰ্থ দেখার জন্য। কিন্তু এদের মৌলবাদী বলা চলে না, কারণ ধর্মের প্রাথমিক ভিত্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জঙ্গী উৎসাহ এবং বৃহত্তর ক্ষমতা লাভের ব্যাপকতর আকাঙক্ষা এদের মধ্যে অনুপস্থিত।
বিশুদ্ধ মৌলবাদী সংগঠন প্রথম গড়ে ওঠে আমেরিকায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ও আরো সুনির্দিষ্টভাবে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে, ফান্ডামেন্টালিস্টদের মধ্যে। বাইবেল তথা ধর্মের মাহাত্ম্যকে প্রতিষ্ঠা করার প্রাথমিক তীব্রতা এদের অস্তিত্ব জুড়ে সম্পৃক্ত ছিল। অবধারিতভাবে শ্রেণীস্বার্থ তার সঙ্গে জড়িয়ে ছিলই, কিন্তু তা প্রধানভাবে প্রকাশ পায় আরো পরে যখন বিবর্তনবাদ ছাড়িয়ে কম্যুনিজমকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারটি সুনির্দিষ্ট মাত্রা পায়। এখনকার মৌলবাদী সংগঠনের মধ্যে এই দিকটি একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।
নিয়ানডার্থাল মানুষেরা শেষের দিকে ঐশ্বরিক শক্তি ও আত্মজাতীয় কোনকিছুর কল্পনা শুরু করলেও এবং পরবর্তী কালের আধুনিক মানুষ (হোমো স্যাপিয়েন) তার ক্রমশ বিকশিত ধারাবাহিকতা বজায় রাখলেও, এগুলি সাংগঠনিক ভাবে বিশেষ প্রতিষ্ঠানিক ধর্মের রূপ পায় আরো হাজার হাজার বছর পরে,-মাত্র ৫-৬ হাজার বছর আগে, যখন শ্রেণী বিভক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে, বিভিন্ন প্রাচীন ধর্ম (যেমন মায়া আজটেকদের) গড়ে ওঠে। এসব ধর্মের প্রায় সবগুলিই এখন অবলুপ্ত, জাদুঘরে ও ঐতিহাসিকদের কাজে কর্মে তা টিকে আছে। পরবর্তীকালে বৈদিক ধর্ম, ইহুদি ধর্ম, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম, খৃস্টধর্ম, হিন্দুধর্ম, ইসলাম ধর্ম, শিনটো ধর্ম, কনফুসিয়াসের ধর্ম (বা মতবাদ), শিখ ধর্ম, বাহাই ধৰ্ম ইত্যাদি নানা ধর্ম গড়ে ওঠে। এ ব্যাপারে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। লেখকের ‘ধর্মের উৎস সন্ধানে (নিয়ানডার্থাল থেকে নাস্তিক)’ গ্রন্থে, ২য় সংস্করণ, প্রবাহ, কলকাতা-৯]
এই সব ধর্মের কারোর অবলুপ্তি, কারোর অজস্র বিভাজন, কারোর নানা ভাঙ্গা গড়া উত্থান পতনের ব্যাপারগুলি এটি প্রমাণ করে যে, এগুলি চিরন্তন বা সনাতন যেমন আদৌ নয়, তেমনি তা সম্পূর্ণ মনুষ্যসৃষ্ট, মানুষেরই প্রয়োজনে তৈরী হওয়া। এই প্রয়োজনেই সময়ের সঙ্গে তাদের পরিমার্জনা ও রূপান্তরও ঘটেছে, যেমন বৈদিক ধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মের স্তর পেরিয়ে এক সময় তথাকথিত হিন্দুধর্মের রূপ পেয়েছে, যদিও, এইভাবে পরিচিত হওয়ার ব্যাপারটা নিতান্তই হাল আমলের ঘটনা-বৃটিশ শাসনকালে। মৌলবাদীদের নিয়ে মুস্কিল হচ্ছে, তারা এই সময়োপযোগী রূপান্তর ও পরিমার্জনার ব্যাপারটাকে অস্বীকার করে এবং ধর্মের প্রাচীন রাপের সুবিধাজনক দিকগুলিকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।
এই মৌলবাদ ও মৌলবাদীরা ধর্মের সৃষ্টি বহু পরে জন্ম নিয়েছে, যদিও তারা দ্রুণাকারে ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে বর্তমান ছিল। ধৰ্মীয় মৌলবাদের (এবং সাম্প্রদায়িকতারও) পূর্ববর্তী একটি অবস্থা ধর্মান্ধতা বা ধর্মীয় গোঁড়ামি (religious famaticism)। সমস্ত ধরনের যুক্তির পথ পরিহার করে ধর্মের অনুশাসন, রীতিনীতি ইত্যাদিকে যান্ত্রিকভাবে বিশ্বাস করা ও তাকে কাজে প্রয়োগ করা ধর্মান্ধতার প্রধানতম দিক; এর জন্য ধর্মান্ধতা বা গোঁড়ারা অন্যের ধর্মবিশ্বাসকে বা ধর্ম বিশ্বাসের গণতান্ত্রিক অধিকারকে আঘাত করতে দ্বিধা করে না, এমন কি তাদের শত্রুর পর্যায়েও ফেলে দেয়।
হিন্দুরা বৌদ্ধদের উপর, মুসলিমরা হিন্দু বা বৌদ্ধদের উপর, ইহুদি-খৃস্ট মুসলিমরা পরস্পরের উপর যে অত্যাচার ও নিপীড়ন একদা চালিয়েছে তা ধর্মনিষ্ঠ বা মৌলবাদী মানসিকতা কোনটি থেকেই নয়, এই ধর্মান্ধতা থেকেই এবং কখনো কখনো তার সঙ্গে তীব্র ধর্মীয় পুনরভ্যুত্থানবাদও মিশে ছিল। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় যখন একদল খেটে খাওয়া মানুষ তারই মত মেহনতী কিন্তু ভিন্ন ধর্মের মানুষের উপর হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে খুন থেকে ধর্ষণ-নানা ধরনের অত্যাচার চালায়, তখন তার মধ্যে যুক্তি বোধহীন ধর্মান্ধতার ব্যাপারটিই বেশি থাকে,-যে ধর্মান্ধতা হিংস্র৷ সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দিয়েছে।
নিছক ধর্মবিশ্বাস ধর্মান্ধতায় পরিণত হয়। মূলত তখনি যখন মনে করা হয় যে, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা তার ধর্ম, তথা তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে, তার অর্থনৈতিক ও সামাজিক শ্রেণী স্বাৰ্থ বিঘ্নিত হচ্ছে। এরই একটি বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিক্রিয়ায় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সৃষ্টির সময় খৃষ্টপূর্ব প্রায় পঞ্চম শতাব্দী সময়কালে; তখন ব্রাহ্মণের বৌদ্ধ বা জৈনদের নাস্তিক নামে গালাগালি করেছে। কিংবা আরো আগে যখন বৈদিক ধর্মের বিপরীতে চার্বক বা বাৰ্হস্পত্য দর্শনের সৃষ্টি হয়েছে; তখন বেদ-ব্ৰাহ্মণের রক্ষকেরা চার্বকদের পুড়িয়ে মেরেছে। (মহাভারতে যুধিষ্ঠিরের রােজ্যাভিষেকের সময়কার এই পুড়িয়ে মারা: বর্ণনা হয়তো প্রতীকী ছিল, কিন্তু তার মধ্যে চাৰ্ব্বকদের বিরুদ্ধে যুক্তিহীন ধর্মািন্ধাদের হিংস্রতার পরিচয়ও ফুটে ওঠে।)
বিশেষ প্রতিষ্ঠানিক ধর্মে নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের ব্যাপারটিতে ধর্মান্ধতা নমনীয়রূপে লুকিয়ে থাকে। তা যদি না থাকে। তবে বিশেষ একটি ধর্মে বিশ্বাসের ব্যাপারটিরই অস্তিত্ব থাকে না এবং তার বিশেষ আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, মূল্যবোধকে একনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করারও তাগিদ থাকে না। হিন্দু হলে গরুর মাংস বা মুসলিম হলে শুয়োরের মাংস একেবারেই খাব না-এটি একটি নির্দোষ ধর্মান্ধতার হাস্যকর রূপ। আগেকার দিনের ব্রাহ্মণেরা বা মুনি-ঋষিরা বা হিন্দুদের ‘দেবদেবীরা’। যে আকছারই গরুর মাংস খেত, এমনকি কৃষ্ণ যজুর্বোেদ ব্রাহ্মণকে যে গরুর মাংস দিয়ে আপ্যায়ন করারও নির্দেশ দেওয়া আছে, কিংবা নিছক অর্থনৈতিক কারণেই যে গো-সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছিল এবং গরুকে ‘মা’ হিসেবে (অর্থাৎ হিন্দুদের ‘বাছুর’ হিসেবে) ভাবাটা যে কোন কাজের কথা নয়-এ ধরনের সামান্য যুক্তিবোধও প্রয়োগ করা হয় না। একই ভাবে হজরত মহম্মদ যাদের মুসলিম হিসেবে ধর্মস্তিরিত করেছিলেন, তারা যে ধর্মস্তিরিত হওয়ার আগে শুয়োরের মাংসও খেত, কিংবা যথাসম্ভব স্থানীয় শত্ৰু-স্থানীয় মানুষেরা শুয়োর পুষত বলে মুসলিমরা শত্রুদের পোষ্য জীবকে ঘূণ্য হিসেবে প্রচার করেছে অথবা ‘আল্লার সৃষ্টি করা’ গরু-ছাগল খেতে পারলে শুয়োরই বা কেন খাওয়া যাবে না–এ ধরনের কোন কথাবার্তা শোনাও কানে আঙ্গুল দিয়ে বন্ধ করা হয়।
এই ধরনের যুক্তিবিবর্জিত বিশ্বাসের মানসিকতাই (যা প্ৰতিষ্ঠানিক ধর্মের অসংখ্য বাহ্যিক চরিত্রকে বিশিষ্টতা দান করে) এক সময় উগ্র আকার ধারণ ক’রে ধর্মান্ধিতা ও ধর্মীয় গোঁড়ামির পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করে।’* এর জন্য নিজে শহিদ হওয়া ও অন্যদের শহিদ হতে উৎসাহ দেওয়ার কাজ অনায়াসে করা হয়। প্রতিবেশী হিন্দু বা মুসলিমকে খুন করলে, নিজের স্ত্রী বা কন্যার মত এক ভিন্নধর্মাবলম্বিনীকে ধর্ষণ করলে বা ভিন্ন ধর্মের মানুষদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলে যে আদৌ নিজের ধর্মের প্রতি শ্ৰদ্ধা প্ৰকাশ করা হয় না এবং নিজেদের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক সমস্যাবলীরও সুরাহা হয় না, এ ধরনের যুক্তিবোধ ধর্মান্ধতাদের মধ্যে থাকে না।
ধর্মান্ধতারা নিজেদের অর্থনৈতিক আন্দোলনকে ধর্মের সঙ্গে গভীরভাবে মিশিয়েও দেয়। ধর্মই যে অর্থনৈতিক বৈষম্যকে বাড়িয়ে তোলার ও টিকিয়ে রাখার অন্যতম একটি উপায় তা ধর্মান্ধিরা মাথাতেও আনে না। এই ভাবেই ধর্মান্ধতারা নিজ ধর্মের সমস্ত মানুষের সব ধরনের স্বার্থকে অভিন্ন বলে ভাবতে শুরু করে। এই মানসিকতা তীব্রতা পায় সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের মধ্যে।
বিভিন্ন ধর্মে বিভিন্ন পরিবেশে এই রূপান্তর ঘটে। তবে ধর্মান্ধতা বিশেষ সময়ে ধর্মীয় পুনরভ্যুত্থানবাদ (religious revivalism)-এরও জন্ম দেয়। এই পুনরভ্যুত্থানবাদের সৃষ্টি হয় মূলত ঐতিহ্যশালী ধর্মীয় মূল্যবোধ যখন বিশেষ কালে নানা প্রশ্ন ও বিরোধী যুক্তির সম্মুখীন হয় এবং তার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে বলে মনে করা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে হিন্দু ধর্মীয় পুনরভ্যুত্থানবাদীদের অভ্যুত্থান এই বাংলায় ঘটেছিল। এইভাবেই। তার আগেইয়ংবেঙ্গল থেকে বিদ্যাসাগরের মত ব্যক্তিরা সনাতন হিন্দু ধর্মের জঞ্জাল ও ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯–১৮৩১)-র মুক্তমন ও যুক্তিবাদী মানসিকতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মূলত সমাজের উপরতলার হিন্দুপরিবারের সন্তানেরা ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনকে একটি শক্তিশালী রূপ দান করেন। প্রকাশ্যে গোমাংস ও মদ্যপান করা জাতীয় কাজকে ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করার একটি উপায় হিসেবে ভাবা হয়েছিল। (যদিও জনসাধারণের সর্বস্তরে মতাদর্শগত ব্যাপক প্রচার না চালিয়ে ও আর্থ সামাজিক অন্যান্য দিকের সঙ্গে তাকে যুক্ত না করে, বিচ্ছিন্ন ভাবে করা এসব কাজে ব্যক্তিগত ‘হিরোইজম’-ই ছিল বেশি; সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে এমন কাজ ধর্মাচরণকে আরো নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকড়ে ধরার প্রবণতাও সৃষ্টি করে।) অন্যদিকে রামতনু লাহিড়ি (১৮১৩–১৮৯৮) প্রকাশ্যে উপবীত ত্যাগ করেন (১৮৫১ সালে) বা রসিককৃষ্ণ মল্লিক (১৮১০-১৮৫৮) আদালতে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে গঙ্গজলের পবিত্রতা অস্বীকার করেন। ডিরোজিয়ানদের এমন কাজকর্ম সুবিদিত এবং তা সমাজে উল্লেখযোগ্য আলোড়নও যে ফেলেছিল তাতেও কোন সন্দেহ নেই। পাশাপাশি ঈশ্বরচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগরের (১৮২০–১৮৯১) মত ব্যক্তিত্বরা ডিরোজিয়ান না হলেও হিন্দুধর্মীয় আবিলতার বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্ৰ চিঠিপত্রের শিরোনামে লোকচারবশত ‘শ্ৰী শ্ৰী হরিঃ শরণম শ্ৰী শ্ৰী হরিঃ’, ইত্যাদি লিখলেও ধর্ম ও ঈশ্বর-বিশ্বাসের প্রতি তাঁর কোন মোহ ছিল না। তাই দ্বিধাহীনভাবে তিনি এটি জানিয়েছেন, ‘বেদান্ত ও সাংখ্য যে দর্শনের দুটি ভ্ৰান্ত ধারা এ ব্যাপারে আর তর্কের অবকাশ নাই। এগুলি মিথ্যা হলেও হিন্দুদের কাছে অপরিসীম শ্রদ্ধা পায়।’ (‘That the Vedanta and Sankhya are false systems of philosophy is no more a matter of dispute. These systems, false as they are, command unbound reverence from the Hindus.’–কাউন্সিল অব এডুকেশনের সেক্রেটারি এফ আই মুয়াট-কে লেখা চিঠি, ৭ই সেপ্টেম্বর ১৮৫৩)। অন্যদিকে সাংগঠনিকভাবেও হিন্দুধর্মের উপর আঘাত আসে ব্রাহ্মধর্ম সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। (ব্রাহ্ম সমাজ বা ব্রাহ্মসভার প্রথম অধিবেশন হয় ১৮২৮-এর ২০শে অগাস্ট।)
এগুলি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। তখনকার বাঙলার শিক্ষিত সমাজে মুক্তমন ও সংস্কারের যে পরিমণ্ডল তৈরী হয়েছিল তার বহিঃপ্রকাশ এসব। নতুন ইয়োরোপীয় জ্ঞান ও আধুনিক মননের সঙ্গে পরিচয় এই মুক্তমন গড়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছিল। কিন্তু হিন্দুধর্মের চিরাচরিত। ঐতিহ্যের প্রতি এ ধরনের আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় এবং ব্রাহ্মধর্ম ছাড়া খৃষ্টধর্মের দ্বারাও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে, ধর্মীয় পুনরভ্যুত্থানবাদী মানসিকতাও সৃষ্টি হয়। এই চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল, অবৈজ্ঞানিক মানসিকতা রূপ পায় শশধর তর্কচূড়ামণি (১৮৫১-১৯২৮)-র মত মানুষদের মধ্যে। একদিকে ইনি যেমন সহবাস-সম্মতি আইন’ প্রণয়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনা করেন, তেমনি হাঁচি-টিকটিকির বাধানিষেধ জাতীয় হাস্যকর কুসংস্কারগুলিরও ‘বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা’ দিয়ে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নেতৃত্ব দিতে থাকেন। অন্যদিকে গদাধর চট্টোপাধ্যায় তথা শ্ৰীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব (১৮৩৬–১৮৮৬) ও তার ভাবশিষ্য নরেন্দ্রনাথ দত্ত তথা স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩–১৯০২)-এর মত বর্তমানে অতি প্রভাবশালী ধর্মীয় নেতা ও সংস্কারকরাও হিন্দুধর্মের ঐ টালমাটাল অবস্থায় নব্যহিন্দুত্বের (NeoHinduism) এক উদার চিস্তার প্রচার করেন। ঈশ্বরচন্দ্ৰ যাকে ভ্ৰান্তদর্শন বলেছিলেন সেই বেদান্ত আর ভক্তিবাদ তাদের এধরনের প্রচারে বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল। পুনরভ্যুত্থানবাদীদের সমস্ত বৈশিষ্ট্য তাঁদের মধ্যে না থাকলেও ‘অভ্যুত্থানমধৰ্মস্য’–এর প্রতিক্রিয়ায় তাদেরও সৃষ্টি।
এই তথাকথিত অধর্মের অভ্যুত্থানের প্রতিক্রিয়া বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮– ১৮৯৪)-এর মত পণ্ডিত সাহিত্যসম্রাটের লেখাতেও প্রতিফলিত হয়। তিনি শুধু হিন্দুত্ব ও কৃষ্ণতত্ত্বের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষাস্ত হননি, আনন্দমঠ’-এর মত উপন্যাসের মধ্য দিয়ে হিন্দুত্ববাদী মানসিকতারও প্রচার করেন, যা ঐ পরিবেশে হিন্দু পুনরভ্যুত্থানবাদের কাছাকাছিই বা সমার্থক ছিল। এমন কি আনন্দমঠের প্রথম দিকের সংস্করণে বৃটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা থাকলেও, পরে বৃটিশ তোষণের জন্য, তথা নিজের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও শ্রেণীস্বার্থ অক্ষুন্ন রাখতে, এসব কথা পাল্টে তার পরিবর্তে ‘নেড়ে।’ তথা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘূণার বীজ বপন করেন। দু’তিন হাজার বছর আগে বহিরাগত তথাকথিত আর্যরা যেমন ভারতের আদিবাসিন্দাদের সঙ্গে লড়াই করে পরে একাত্ম হয়েছিল, তেমনি কয়েকশত বছর আগে মুসলিমরাও ভারতে পদার্পণ করে একসময় এদেশেরই লোক হয়ে গেছে। আর বর্তমানের মুসলিম জনসংখ্যার বৃহদংশ এ দেশেরই ধর্মান্তরিত মানুষ। তবু এই ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করে, এখনকার হিন্দু মৌলবাদীদের মত, বঙ্কিমচন্দ্রও ‘মুসলিমদের বিদেশী হিসাবে দেখিয়েছিলেন, এবং জাতীয়তাবাদ বা ভারতীয়ত্ব বা দেশজ-সবকিছুর হিন্দুত্বের সঙ্গে অভিন্ন রূপ কল্পনা করেছিলেন।’ (আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতা, বিপান চন্দ্র)। এইভাবেই ধর্মীয় পুনরভ্যুত্থানবাদীরা-ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ও মৌলবাদের সূত্রপাত ঘটায়, যে সাম্প্রদায়িকতা আমাদের দেশে আগে এভাবে জনমানসে প্রতিষ্ঠিত ছিল না।
জাতীয়তা ও স্বদেশ প্রেমের নামে এমন হিন্দু ধর্মীয় পুনরভ্যুত্থানবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা একাকার হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি শুধু বঙ্গদেশে নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ভারতীয় ভূখণ্ডেই মাথা চাড়া দিতে শুরু করে। বাল গঙ্গাধর তিলকের মত কিছু অসাধারণ দক্ষ, এমনকি দেশপ্রেমিকের হাতে তার সূচনা। তবে তিলকের দৃষ্টিভঙ্গীতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলি অবশ্যই প্রাধান্য পেত, কিন্তু এটিও সত্য যে, ‘তিলক তঁর হিন্দু ধর্মীয় ভাবসম্পন্ন গণেশ পূজা এবং শিবাজী উৎসব প্রচারের মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয়তাবাদে হিন্দুত্বের সংশ্লেষ বৃদ্ধিতে উৎসাহ দিয়েছিলেন’ এবং অন্যদিকে ‘অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন চন্দ্ৰ পাল এবং লালা লাজপত রাই প্রমুখ চরমপন্থী নেতারা তাদের রাজনৈতিক বক্তৃতা ও রচনায় হিন্দুপ্রতীক, বাকরীতি ও পুরাণকে ব্যবহার করতেন। ভারতকে অনেক সময়ে মাতৃদেবী বলে উল্লেখ করা হত, বা কালী, দুর্গ ও অন্যান্য হিন্দু দেব-দেবীদের সঙ্গে তুলনা করা হত।’ (ঐ) এটি অবশ্যই ঠিক যে, এই সব নেতৃবৃন্দ বা তাদের কাজকর্মকে সরাসরি ধর্মীয় পুনরভ্যুত্থানবাদী বা সাম্প্রদায়িক বলা যায় না। কিন্তু তারা, হয়তো বা অসচেতনভাবেই এবং মুসলিমদের প্রতি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ পোষণ না করেই, এই ধর্মীয় পুনরভ্যুত্থান ও সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে গেছেন। এখনো আমাদের দেশে এই সব নেতৃবৃন্দকেই পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রচার করা ও মহীয়ান করা হয়। তাদের অবদানের প্রাপ্য মর্যাদা অবশ্যই দেওয়া উচিত, কিন্তু রাষ্ট্রীয় স্তরে তাদের অন্যদিকগুলিকে অস্বীকার করে বিশুদ্ধ ভক্তি ও সন্দেহাতীত মহত্ব প্রচারের মানসিকতা থেকে বর্তমান রাষ্ট্রীয় চরিত্রটিকে আঁচ করা যায়।
ঘটনাচক্ৰে অথবা হয়তো কোন বিশেষ ঐতিহাসিক আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে (যে ক্ষেত্রে বিবর্তনবাদ(২) থেকে মার্ক্সবাদের মত নানা বৈজ্ঞানিক চিন্তার উদ্ভব হয়তো ভূমিকা পালন করেছে), বাংলায় তথা ভারতে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই ধর্মীয় পুনরভু্যত্থানবাদীদের উদ্ভবের সময়ে আমেরিকাতেও সৃষ্টি হচ্ছিল ফান্ডামেন্টালিজম-এর ভিত্তি। এর আগেই বলা হয়েছে। ইয়োরোপে সংগঠিতভাবে ধর্মীয় পুনরভ্যুত্থানবাদ (Revivaism) সৃষ্টি হয়েছিল আরো আগে,-অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। এর একটি কারণ নিশ্চয়ই এই যে, মুক্ত চিন্তা, ধর্মীয় কুসংস্কারগুলির উপর আঘাত করা এবং ধর্মের ভিত্তিটিকেই নাড়া দেওয়ার কাজটি ইংল্যাণ্ডে তথা ইয়োরোপে শুরু হয়েছিল ভারতের থেকে অনেক আগে। প্ৰতিদেশে সব সময়েই এই স্রোতবিরোধী ধারা লোকচরিত্রের একটি অংশ। কিন্তু কখনো কখনো তা বিশেষ মাত্রা পায়। ইংল্যাণ্ডে সপ্তদশ শতাব্দীতে তো বটেই এমন কি পঞ্চদশ শতাব্দীতেও ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কাজকর্মের উদাহরণ কম নেই। ১৪৯১-তেই এক ছুতোর দীক্ষাস্নান, স্বীকারোক্তি ইত্যাদি প্রথাকে মেনে নিতে অস্বীকার করে। তখন বিশেষত যাজকতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিশেষভাবে দানা বাঁধে। লোলার্ড গোষ্ঠীর একজন মন্তব্য করেছিলেন, ‘ধর্মযাজকেরা জুডাস-এর থেকেও খারাপ। জুডাস তিরিশ পেন্সের জন্য যিশুকে ধরিয়ে দিয়েছিল। যাজকেরা তো আধাপেনির বিনিময়ে মানুষকে দলে দলে বিকিয়ে দিচ্ছে।’ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানবিরোধী এ ধরনের অজস্র আন্দোলন ও মতামত ক্রমশঃ বিকশিত হয়েছে এবং সপ্তদশ শতাব্দীর আসন্ন পুঁজিবাদী বিপ্লবের রাস্তা মসৃণ করেছে। একদিকে ধর্মীয় ক্ষেত্রে যেমন পুরনোকে ছেড়ে নতুন পথ খোঁজার চিন্তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (আর তার নেতৃত্ব মূলত দিয়েছে ইংল্যাণ্ডের নীচুতলার পছিয়ে থাকা নিপীড়িত মানুষরাই), তেমনি অন্যদিকে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও নিত্যনতুন আবিষ্কার ও সত্যের সন্ধান শুরু হয়েছে, যার একটি ফলশ্রুতি প্রগতিশীল পুঁজিবাদের উদ্ভব তথা শিল্প বিপ্লব। ধর্মীয় ক্ষেত্রে ডিগার, র্যান্টার, ফ্যামিলি পন্থা, লেভেলার, কোয়েকার ইত্যাদির মত প্রতিবাদী গোষ্ঠীগুলির নেতৃত্ব মূলত এসেছিল জনসাধারণের দরিদ্র পিছিয়ে পড়া অংশ থেকেই।
ধর্মের অস্তিত্বের সংকটের সময়ে (অন্তত যখন এই সংকট সৃষ্টি হয়েছে বলে ভাবা হয়), তখন সম্ভবামি যুগে যুগে’-র এই ধর্মীয় পুনরভ্যুত্থানবাদ থেকে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। পুনরভ্যুত্থানবাদের মধ্যে ধর্মের বিপন্ন অস্তিত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার আকাঙক্ষাই প্রধানতম। বিশুদ্ধ ধর্মীয় পুনরভ্যুত্থানবাদীরা লড়াই করে তাদের বিরুদ্ধে বা সেই চিন্তা ও শক্তির বিরুদ্ধে যারা বা যা তাদের ধর্মকে হতমান করে অথবা যখন সামগ্রিক ভাবে ‘ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি’। এক্ষেত্রে বিশেষ ভিন্ন ধর্ম এই ভূমিকা পালন করলে তার বিরুদ্ধেও লড়াই চলে, অন্যথায় সাধারণভাবে এর মধ্যে বিশেষ সম্প্রদায়কে হেয় করা বা আপন সম্প্রদায় থেকে পৃথক করার মানসিকতা বিশেষ গুরুত্ব পায় না। পুনরভ্যুত্থানবাদীদের মধ্যে ধর্মের শ্রেণীগত স্বাৰ্থ সংশ্লিষ্ট থাকলেও, ধর্মপ্রতিষ্ঠার আপাত সদিচ্ছার তুলনায় তা গুরুত্বপূর্ণ নয়।
কিন্তু ধর্মীয় পুনরভুত্থানবাদের তীব্রতা প্রায়শই তার এই নিছক ধর্মমাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার আকাঙক্ষাকে ছাড়িয়ে সম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়, অন্তত তাদের জন্মদাতার ভূমিকা পালন করে। ধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার যুক্তিহীন আবেগ প্রায়শঃই পুনরভ্যুত্থানবাদীদের নিজ ধর্মকে সর্বশ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার, আপন ধর্মের মূল নিষ্কলুষ অবস্থাকে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করার ও বিরুদ্ধবাদী চিন্তাকে হিংস্রভাবে মোকাবিলা করার দিকে ঠেলে দেয়, অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী করে তোলে। ইয়োরোপে প্রোটেস্টাণ্টদের মধ্যে অষ্টাদশ শতকে উদ্ভূত রিভাইভ্যালিজম উত্তর আমেরিকায় প্রসারিত হওয়ার পর, ঊনবিংশ শতকে ফান্ডামেন্টালিজ সৃষ্টির পথকে সুগম করেছে; অবশ্যই এক্ষেত্রে বিবর্তনবাদ ও মার্কসবাদ জাতীয় বৈপ্লবিক চিন্তা ইন্ধন জুগিয়েছে এবং ক্রমশঃ পরিবর্তিত অর্থনৈতিক অবস্থায় নতুনতর মাত্রার শ্রেণীদ্বন্দ্ব অনুঘটকের কাজ করেছে।
একসময় ভারতীয় ভূখণ্ডেও হিন্দু ও মুসলিম এই দুই প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠী দীর্ঘদিন ধরে মোটামুটি শান্তিপূর্ণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের অবস্থায় কাটিয়েছে। উভয়ের নানাবিধ ধর্মীয় উৎসব, ধর্মীয় সংস্কার ও অন্যান্য চিন্তাভাবনাকে উভয়েই গ্ৰহণ করেছে। মহররমের তাজিয়া ও মহরম হিন্দুদের কাছেও কম আনন্দদায়ক ছিল না। এমন কি অনেক স্থানে অনেক হিন্দু মেয়েদের মধ্যে এমন বিশ্বাসও ছিল যে, তাজিয়ার নীচ দিয়ে হাঁটলে তারা সন্তানের মা হবে। পীরবাবার কাছে মানত শুধু মুসলিমরা নয়, জন্মসূত্রে যারা হিন্দু তারাও করত। দুর্গাপূজা বা কালীপূজার মত হিন্দু ধর্মীয় উৎসবে ও মেলায় মুসলিমরা,-পূজা না দিক, পৌত্তলিকদের অনুষ্ঠান বলে না। সরে গিয়ে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করত। অশ্বখগাছের তলায় ঠাকুরের থানে মানত করে বা ঢ়িল বেঁধে নিঃসন্তান মুসলিম রমণীরাও তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণের চেষ্টা করত। হিন্দু-মুসলিম সাংস্কৃতিক ঐক্যের এই অতি স্বাভাবিক সামাজিক ধারা এখনো নেই তা নয়’(৩), কিন্তু উভয়ের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভেদের মানসিকতা যে ব্যাপকতা লাভ করেছে। ঐ ব্যাপকতা আগে (অন্তত ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পূর্বে) মোটেই ছিল না। উচ্চবর্ণীয় হিন্দুরা মুসলিমদের অস্পৃশ্য ভেবেছে কিংবা মৌলানা-মৌলবীর মত উচ্চস্তরের মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের কেউ কেউ হয়তো কঠোরভাবে পৌত্তলিক ধর্মানুষ্ঠান পরিহার করেছে, কিন্তু সাধারণভাবে সমাজে উভয়ের মধ্যে ঘূণা-হিংসা-বৈরিতা ছিল না এবং তাই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মত ঘটনায় নীচুতলার হিন্দু-মুসলিম প্রতিবেশীদের অন্তত বৃহদাংশের মধ্যে পরস্পরের বিরুদ্ধে হত্যা থেকে ধর্ষণের মত ক্রিয়াকাণ্ডে লিপ্ত হওয়ার মানসিকতাই অনুপস্থিত ছিল। ভারতের পূর্ব থেকে পশ্চিম সর্বত্রই এই চিত্র কমবেশি ছিল। তাই পাঞ্জাবের ১৮৮১-এর আদমসুমারীর উপর ডেনজিল ইবেটসন-এর গবেষণামূলক রচনায় এমন মন্তব্য দেখা যায়, ‘বাস্তব ক্ষেত্রে পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলে ধর্মান্তর ধর্মািন্তরিতের জাতের উপর কোন প্রভাব ফেলে না। মুসলমান, রাজপুত, গুজার, বা জাট সমস্ত সামাজিক, উপজাতিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে তার হিন্দু ভাইদের মতই একজন রাজপুত, গুজার বা জাট। তার সামাজিক প্রথা অপরিবর্তিত, তার উপজাতিক বাধনিষেধের শৃঙ্খল শিথিল হয় নি, তার বৈবাহিক ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত নিয়ম অপরিবর্তিত;… … …’ ইত্যাদি।
মূলত ইংরেজদের দ্বারা চিহ্নিত ঐ তথাকথিত ইসলামী আমল থেকেই এই ধর্মপরিচয়কে পাত্তঃ-না-দেওয়া সামাজিক বন্ধুত্ব মোটামুটি ছিলই। কিন্তু ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে জাতীয়তাবাদের নামে হিন্দুত্বের পুনরভ্যুত্থানবাদী ক্রিয়াকাণ্ড সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে অভিন্ন হতে থাকে। বৃটিশরা নিজ স্বার্থে এই ধর্মীয় বিভাজন ও বিদ্বেষের বীজ বপন করতে থাকে,-এটি একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যাপার হলেও কোন সহায়ক ভিত্তি না থাকলে ইংরেজদের পক্ষেও এই সাম্প্রদায়িকতার চাপা থাকা আগুনে হাওয়া দেওয়া সম্ভব হত না। বিপানচন্দ্র। যেমন মন্তব্য করেছেন, ‘জাতীয়তাবাদী উলামাও মুসলিমদের মধ্যে ধর্মীয়, এমনকি সাম্প্রদায়িক পরিচিতি বাড়াতে ও সাম্প্রদায়িকতাবাদের প্রসারে প্রচণ্ডভাবে সাহায্য করেছিলেন’ এবং ‘অনুরূপভাবে, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী দয়ানন্দ, অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পাল এবং অন্যান্যরা ধর্মভাবকে উৎসাহ দিয়েছিলেন এবং এইভাবে পরোক্ষে হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক পরিচিতি বোধকে উৎসাহিত করেছেন।’
ভারতের মাটিতে ঐ উলামা-দিয়ানন্দদের দল যদি না থাকত। তবে ইংরেজদের সাধ্য ছিল না। সাম্প্রদায়িকতাকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার। এরা আপন ধর্মের অভ্যুত্থান ঘটানোর বা মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার নামে সাম্প্রদায়িকতার ও পরবর্তীকালে মৌলবাদের পিতৃত্বের (হয়তো বা অজানিত ভাবে) ‘গৌরব অর্জন করেছে। সমাজের বিশেষ কিছু অর্থনৈতিক অবস্থানের মানুষেরা (যেমন বিপন্ন অস্তিত্বের জমিদার গোষ্ঠী, নতুন গজিয়ে ওঠা গ্ৰাম্য জোতদার শ্রেণী, মহাজন, ব্যবসায়ী ইত্যাদিরা) নিজেদের সংকীর্ণ শ্রেণী:স্বাৰ্থ বজায় রাখতে তথা সম্পদ-প্রতিপত্তি বাড়াতে রাজনীতির মধ্যে ধর্মের অনুপ্রবেশকে উৎসাহিত ও ব্যবহার করছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিজীবীদের বৃহদংশ এদের মধ্য থেকেই উঠে এসেছিল; এরাই শিক্ষাদীক্ষা, রাজনৈতিক মতাদর্শ গঠন, সংবাদপত্র প্রকাশনার মাধ্যমে জনমত গঠন, ইত্যাদির নেতৃত্ব দিত এবং এরাই হাতের কাছে ধর্মকে পেয়ে তাকেই বা অন্য কিছু না পেয়ে ধর্মকেই ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। এরা স্বাভাবিকভাবেই বুঝেছিল যে, সাধারণ মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে ভাঙ্গিয়ে নিজের নেতৃত্ব ও শ্রেণীস্বার্থ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। কারণ, ধর্ম যে যুক্তিবোধহীন আনুগত্য, অবৈজ্ঞানিক বিশ্বাস তথা সমাজ সম্পর্কে শ্রেণীসচেতনতা-মুক্ত ধারণাবলীর শিক্ষা দেয়, ঐ সব শিক্ষা সমাজের উপরতলার ব্যক্তিদের স্বাৰ্থপুষ্ট করার ক্ষেত্রে সঙ্গতিপূর্ণ।
এইভাবে ধর্মকে ধনী-দরিদ্রদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের স্তর থেকে নামিয়ে তারা রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা শুরু করে। তারা এমন মানসিকতাকে সুকৌশলে প্রতিষ্ঠা করতে থাকে যে, মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের প্রধানতম দিক হচ্ছে ধর্মপরিচয়, তাই নিজ অস্তিত্বের স্বার্থে ধৰ্মরক্ষা প্রয়োজন এবং আপনি ধর্মের সবাই সুহৃদ, তাদের সবার স্বাৰ্থ এক। অর্থাৎ বিশুদ্ধ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি শুরু হয়। স্বদেশের ও নিজ ধর্মের শাসকশ্রেণীর উপর সামান্য আঘাত না করে শুধু বৃটিশদের হটিয়ে দেশের দরিদ্র জনসাধারণের লাভ যে আসলে বিশেষ কিছুই হবে না—এ বোধকে জগতে না দিয়ে, এই সামন্ত ও উঠতি পুঁজিপতি গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা দেশবাসীর মনে এই বোধকেই প্রতিষ্ঠিত করল যে, বিদেশী ও স্বদেশী উভয় শাসককে নয়, শুধু বৃটিশদের হঠানোই একমাত্র কাজ তথা স্বাধীনতা আন্দোলন ও জাতীয়তাবাদ। এই শ্রেণী নিতে চেয়েছিল বিদেশী শাসক হটিয়ে স্বদেশী শাসকের ভূমিকা এবং তথাকথিত স্বাধীনতা আন্দোলনের পর তাই-ই হয়েছে। এই লক্ষ অর্জনের ক্ষেত্রে জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করতে তারা বিশেষ ধর্মকেই সুবিধাজনক মাধ্যম হিসেবে অনুভব করেছে ও গ্রহণ করেছে। তাই বঙ্কিমের ‘বন্দেমাতরম’ হিন্দু-গন্ধে ভরা, গান্ধীর স্বাধীনতা আন্দোলন হিন্দুরসে জারিত (শত ঐক্যের কথা বলেও) এবং পাকিস্তানকামীদের কাছে তো ইসলাম ধর্মই ছিল একমাত্র ভিত্তি। এইভাবে এরা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে খুচিয়ে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তুলেছে এবং আগুন নিয়ে খেলা করেছে। এখন এ খেলার রিং-মাস্টার হিন্দু-মুসলিম মৌলবাদীরা।
ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে ইংরেজরা ধর্মের ভিত্তিতে ভারতীয়দের বিভাজন ক’রে, তাদের ঐক্য বিনষ্ট করে, শাসন করার কৌশল অবলম্বন করতে থাকে। ম্যালকম (১৮১৩) থেকে এর শুরু। ১৮৫৮-তে লর্ড এলফিনস্টোন বলেছিলেন। ‘ডিভাইড অ্যাণ্ড রুল ছিল প্রাচীন রোমান নীতি এবং আমাদের তা গ্ৰহণ করা উচিত’। ১৮৬২-তে ভারতের রাষ্ট্রসচিব চার্লস উড ভাইসরয়কে জানিয়েছিলেন, ভারতের ‘জাতিগুলির’ অন্তৰ্দ্ধন্দ্বই ভারতে ইংরেজদের শক্তি যোগাবে এবং তাই ‘এই বিভেদকারী শক্তিকে জিইয়ে রাখতে হবে, কারণ সমগ্ৰ ভারত আমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হলে আর কতদিন আমরা টিকে থাকতে পারব?’ ১৮৮৭-তে রাষ্ট্রসচিব ক্রস ভাইসরয়কে লিখেছিলেন, ‘এই ধর্মীয় মনোভাবের বিভাগ আমাদের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক’। ১৯২৫-এ রাষ্ট্রসচিব বার্কেনহেড ভাইসরয়কে লিখেছিলেন, ‘সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি চিরস্থায়ী হোক, সবসময় সর্বান্তকরণে আমি এই আশা রাখছি।’ চাৰ্চিলও এই নীতি অনুসরণ করে গেছেন এবং ভারতের বৃটিশ প্রশাসন মুসলিম সম্প্রদায়কে ‘হিন্দু জাতীয়তাবাদের উল্টো পাল্লার ওজন হিসাবে’ চিরকাল ব্যবহার করে গেছে। হিন্দু ও মুসলিম ধর্মাবলম্বী উভয় সম্প্রদায়ের জাতীয়তাবাদী ‘মহান’ নেতারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই বিলিতি নীতিকে উৎসাহিত করেছেন, — অবশ্যই নিজ স্বার্থে।
ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৃটিশদের আবিষ্কার করা এই ধর্মীয় বিভাজনের পদ্ধতি শক্তিশালী ও উৎসাহিত হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ধমীর্ণয় পুনরভ্যুত্থানবাদীদের দ্বারা। হিন্দু ‘জাতীয়তাবাদী’ ও মুসলিম ‘বিচ্ছিন্নতাবাদীরা’ অনেকাংশে এই শক্তি ও উৎসাহের ফসল।
ধর্মনিরপেক্ষ, শ্রেণী সচেতন, জনগণের নেতৃত্বাধীন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন নয়,-ধৰ্ম-সম্পূক্ত, শ্রেণী-নিরাসক্ত, স্বদেশীয় অভিজাতদের (ভবিষ্যতের শাসকবৃন্দের!!) নেতৃত্বাধীন তথাকথিত বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন, কোন না কোনভাবে সরাসরি বৃটিশ আধিপত্য হয়তো কমিয়েছে, কিন্তু তা একই সঙ্গে দেশবাসীকে দীর্ঘস্থায়ী বৃহত্তর দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে—এই দাসত্ব ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাবাসী মানসিকতার দাসত্ব, যা ক্রমশ মৌলবাদী দৈত্যের জন্ম দিয়েছে। (একই সঙ্গে স্বদেশী সামন্ত পুঁজিপতি ও শাসকশ্রেণীর দাসত্বও।)
ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আর্যসমাজ, হিন্দু মহাসভা জাতীয় নানা হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠন গড়ে ওঠে। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদী জাতীয়তাবাদ ও ধর্মীয় পুনরভ্যুত্থানবাদী ঐতিহ্য-সচেতনতা—এসবের সাংগঠনিক বহিঃপ্রকাশ ছিল এই ধরনের সংস্থার সৃষ্টি। আর্যসমাজ শুরুতে পুরোহিতদের দুর্নীতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে লড়াই করলেও পরে গোহত্যা বন্ধ করা ও উর্দুর পরিবর্তে দেবনাগরী লিপির হিন্দিভাষা প্রচলন করার মত আন্দোলনের দ্বারা এই সময়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করায় যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল। মদনমোহন মালব্য বা লালা লাজপত রাই-এর মত কংগ্রেসী নেতারা হিন্দু মহাসভাতেও সক্রিয় ছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে ১৯৩০-এর দশকের শেষ পর্যন্ত স্থানীয় পর্যায়ে কংগ্রেস এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলির কর্মীরা প্রায় একই ব্যক্তি ছিলেন। পরবর্তীকালে গোলওয়ালকার বা সাভারকর-এর মত হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা তথা মূলগতভাবে মৌলবাদীরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে ও ‘তাদের চর গান্ধীর’ বিরুদ্ধে হিন্দুদের সতর্ক করতে থাকেন। কংগ্রেসী নেতৃত্বের অন্যতম ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিত্ব জওহরলাল নেহরু ১৯৫৮-এর ১১মে কংগ্রেস অধিবেশনে দেওয়া বক্তৃতায় মন্তব্য করেছিলেন,-’সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতা খুব সহজেই ‘জাতীয়’ বলে চালানো যায় এবং সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতাকে বিচ্ছিন্নতাবাদ বলে আখ্যা দিতেও দেরী হয় না।’ প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের শুরুর দিকে এই ধরনের সংখ্যাগরিষ্ঠের সাম্প্রদায়িকতাকেই জাতীয়তাবাদ বলে ভাবা হয়েছে এবং পরবর্তী কালে আর এস এস-বিশ্বহিন্দু পরিষদ-জনসংঘ বা বিজেপি-র মত সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদী হিন্দু সংগঠনগুলি এই মানসিকতাকেই প্রধান ও তীব্রভাবে আঁকড়ে ধরেছে। কংগ্রেস যখন হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা সম্পূক্ত জাতীয়তাবাদকে ধীরে ধীরে পরিত্যাগ বা পরিমার্জিত করেছে, তখন ঐ শূন্যতা পূরণ করতে এগিয়ে এসেছে এই সব হিন্দুত্ববাদীরা।
অন্যদিকে মুসলিমদের একাংশ এক সময় যেমন কংগ্রেসের আপাত সাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদকে ফুলিয়ে ফাপিয়ে বড় করে প্রচার করেছে এবং সাধারণ মুসলিমদের বিভ্রান্ত করেছে, তেমনি পরবর্তীকালে হিন্দুত্ববাদীদের প্রচারের প্রতিক্রিয়ায় নিজেদের আরো সংগঠিত ও জঙ্গী করে তুলেছে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের সৃষ্টি করেছে। মুসলিমদের মধ্যকার এই প্রতিক্রিয়া অনেকটা স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি হলেও, তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে চিহ্নিত করার ও প্রচার করার কাজটিও হিন্দুত্ববাদীরা সুকৌশলে তীব্রতর করেছে। মুসলিমদের অভারতীয়, ভারতীয়তত্ত্বের শিকড় বহির্ভূত, বহিরাগত ইত্যাদি বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এসবের ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ায় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা দেখে তখনকার উগ্ৰ সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে ফ্যাসিবাদের মিল অনেকে(৪) অনুভব করেন। অনেকে এও লক্ষ্য করেন যে ১৯৩৭-এর পর সাম্প্রদায়িকতা নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করছিল, যা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ধর্মীয় মৌলবাদে রূপান্তরের সময় বলে চিহ্নিত করা যায়।
কিন্তু, এই রূপান্তরের পেছনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ছাড়া আরো বহুজনের অতীত ও সাম্প্রতিক ক্রিয়াকাণ্ডও যে ভূমিকা পালন করেছে এবং মৌলবাদী শক্তিকে রসদ জোগানের কাজে অংশগ্রহণ করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। দক্ষিণপন্থীদের মধ্যকার তো বটেই, এমন কি বামপন্থী নামে চিহ্নিত কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি, রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা বুদ্ধিজীবীরা যখন নিজেদের ও সাধারণ মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে রাজনৈতিক ও অন্যান্য স্বাধসিদ্ধির জন্য কাজে লাগাতে থাকে, তখন ধর্মের এই ক্রমরূপান্তর রোধ করা মুস্কিল। এর অর্থ অবশ্যই এ নয় যে, মহাত্মা গান্ধী সহ সামগ্রিকভাবে কংগ্রেসকে এবং বামপন্থীদের সাম্প্রদায়িক বা মৌলবাদী বলা হচ্ছে। এরা সচেতনভাবে ধর্মকে সাম্প্রদায়িক বা মৌলবাদী উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন, তা হয়তো ততটা নয়, যতটা নিজেদের রাজনৈতিক মতাদর্শ ও ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে নিজ ধর্মবিশ্বাস (যেমন মূলত হিন্দু ধর্মে বিশ্বাস), ধর্মীয় পরিচয়, ঈশ্বর বিশ্বাস, বিশেষ ধর্মগ্রন্থের কথাবার্তা ইত্যাদির প্রতিফলনকে সচেতনভাবে পরিহার করার ব্যাপারে অক্ষম হয়েছিলেন। এই অক্ষমতা মৌলবাদ প্রতিরোধে তাদের অক্ষমতারই অংশ।
এবং এইভাবে ধর্মবিশ্বাসের সাম্প্রদায়িক রূপান্তরও ঘটে। ধর্মীয় মৌলবাদী হওয়ার অন্যতম পূর্বশর্ত সাম্প্রদায়িক হওয়া। সব ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা মৌলবাদী নয়, কিন্তু সব ধর্মীয় মৌলবাদীরা অবশ্যই সাম্প্রদায়িক। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, বারংবার বলা দরকার, এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গী, যেটিতে প্রাথমিকভাবে মানুষকে মানুষ হিসাবে গণ্য না করে বিশেষ এক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্য হিসাবেই গণ্য করা হয়। অর্থাৎ মানুষের এই কৃত্রিম ধর্মীয় পরিচয়ই তাদের কাছে প্রধান পরিচয়। উপরন্তু এটি আসলে আপনি ধর্মীয় সম্প্রদায়কে ও ধর্মকে অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে সুস্পষ্টভাবে পৃথক ও শ্রেষ্ঠ হিসেবে প্রচার করার চেষ্টা করে(৫) আর ভিন্ন ধৰ্মসম্প্রদায়ের সবাইকেই শত্রু হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে, এবং অবশ্যই স্বাভাবিকভাবে শ্রেণী:নিবিশেষে আপন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সবার স্বার্থকে অভিন্ন বলে বিশ্বাস করতে শেখায়। মৌলবাদ এসব তো করেই, উপরন্তু সে নিজ ধর্মের বিশুদ্ধ মূল রূপকে (যা অবশ্য বিতর্কিত) পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপরেও জোর দেয়। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কাছে এই ধর্মীয় পুনঃপ্রতিষ্ঠার ব্যাপারটি ততটা গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না। কিন্তু এ দুটি এবং ধর্মীয় পুনরভ্যুত্থানবাদও, ‘নুনচিনির সরবতের মত পরস্পরের সঙ্গে মিশে থাকে, শুধু কখনো নুন বা চিনির মাত্রার হেরফের ঘটে মাত্র। এরা সবাই এটিও প্রচার করার চেষ্টা করে যে, নিজ ধর্মের নির্দেশিত পথেই জনসাধারণের সব সমস্যার সমাধান হবে। যেহেতু এই প্রচার সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ও অবৈজ্ঞানিক, তাই বিপজ্জনকও বটে। এবং প্রকৃতপক্ষে এর মধ্য দিয়ে নিজ সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করে বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী:ই, জনসাধারণ নয়,–তারা শুধু প্ৰতারিত হয় এবং তাদের ধর্মবিশ্বাস এদের হাতে ধৰ্ষিত হয় মাত্র।
সাম্প্রদায়িকতা শুধু ধর্মীয় নয়,-ভাষাগত, জাতিগত, প্রাদেশিক, এমন কি অঞ্চলগত বা গোষ্ঠীগতও হতে পারে। (মৌলবাদ এখনো এত বৈচিত্ৰ্য পায় নি।) এখানেও সাম্প্রদায়িকতার মূল দৃষ্টিভঙ্গী অক্ষুন্ন থাকে। অর্থাৎ এই ধরনের সাম্প্রদায়িকতাও শ্রেণী:স্বার্থের বিভিন্নতা উপেক্ষা করে ও মানুষকে এটি বোঝানোর চেষ্টা করে যে, ভিন্ন ভাষার, জাতির বা প্রদেশের সব মানুষই তার শত্রু (ভাষা আন্দোলনের মত আন্দোলন থেকে ভাষাগত সাম্প্রদায়িকতাবাদের এ একটি বড় তফাৎ), একই ভাষার বা জাতির বা প্রদেশের সবার স্বার্থ এক ইত্যাদি। আমরা বাঙালী’-র মত এমন সংগঠিত সাম্প্রদায়িকতা বা অহমীয়া-উড়িয়া ইত্যাদিদের মধ্যেকার আঞ্চলিক সাম্প্রদায়িকতা দু এক দশক আগেও অনুপস্থিত ছিল। মৌলবাদের পাশাপাশি, এদের সৃষ্টির পেছনেও, সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান সংকট ও বিপন্নতাবোধ এবং ক্ষমতালিঙ্গু বিশেষ গোষ্ঠীর উসকানি প্রধান ভূমিকা পালন করে। বাঙালীদের স্বার্থ বুঝি মারোয়াড়িরাই (বা এ জাতীয় অন্যরা) বিপন্ন করে তুলেছে, এমন ধরনের প্রচার করা হয়। (যেমন করা হয়, ‘হিন্দু বা মুসলিমরা মুসলিম বা হিন্দুদের নানাবিধ সংকটের প্রধান কারণ—’ মুসলিম বা হিন্দু সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদীদের এমন কথাবাতাঁর মধ্য দিয়ে।) আসামে বা উড়িষ্যায়। ‘বাঙালী খেদাও’ কিংবা ইংল্যাণ্ডজার্মানিতে ‘এশিয়ান হটাও’ জাতীয় দেশি-বিদেশী অজস্র উগ্ৰ সাম্প্রদায়িকতাবাদী ফ্যাসিস্ট কায়দার আন্দোলনেও একই কাজ করা হয়। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মত সর্বত্রই এ ধরনের সাম্প্রদায়িকতা এটি ভুলে যায় ও অন্যদের ভুলিয়ে দিতে চেষ্টা করে যে, বেকারত্ব থেকে শুরু করে নানা অর্থনৈতিক সংকটের কারণ কয়েকজন জন্মসূত্রে বাঙালী, মারোয়াড়ী, এশিয়ান বা কৃষ্ণাঙ্গ ইত্যাদিরা নয়; তার প্রধান কারণ লুকিয়ে আছে নিজেদের অক্ষমতা ও অযোগ্যতার পাশাপাশি, প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যেই, যে ব্যবস্থা বৈষম্যভিত্তিক ও শোষণজীবী।
প্রকৃতপক্ষে এইভাবে সাম্প্রদায়িকতার ও মৌলবাদের সৃষ্টির মধ্যে এক সংকটের অনুভবের সঙ্গে হতাশাও মিশে থাকে। যে শাসকশ্রেণী ও সুবিধাভোগী গোষ্ঠী এই সংকট ও হতাশার মূলে তারা তাদের অস্তিত্বের স্বার্থে এই ধরনের সাম্প্রদায়িকতাকে (ও ধর্মীয় মৌলবাদকেও)। মদত দিতে থাকে। কারণ তারা স্পষ্টই অনুভব করে, এবং উল্লসিত ও নিশ্চিন্ত হয় এটি জেনে যে, এই ধরনের আন্দোলনে জনসাধারণ তার মূল শক্রকে চেনার ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তাদের সমস্ত উদ্যম ও উৎসাহ ভিন্নপথে চালিত হয়ে যায়, ফলত প্রকৃত শত্রু যে শ্রেণী ও গোষ্ঠী তাদের উৎখাত করায় জনসাধারণ কখনোই সফল হবে না।
আমেরিকার ফান্ডামেন্টালিস্টরা যখন (পরবর্তীকালের ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মত)। কম্যুনিজম-কে প্রধান শত্রু হিসেবে গ্রহণ করা শুরু করে, তখন তার মধ্যে এদিকটি স্পষ্ট ধরা পড়ে। পরবর্তিত পরিস্থিতির অর্থনৈতিক সংকটে ভীত-সন্ত্রস্ত পুঁজিপতিরা তাদের অস্তিত্বের স্বার্থে কম্যুনিজম রুখতে ফান্ডামেন্টালিজমকে উৎসাহিত করে। এখনো প্রধানতম সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমেরিকায় এর (এবং তার আরো পরিমার্জিত রূপের) অস্তিত্ব এই সুগভীর স্বাৰ্থবোধকে পরিস্ফুট করে। এর ফলে আমেরিকার জনগণের সংকট কমে তো নি, বরং ক্রমবর্ধমান। যে সময়ে আমেরিকার বহুজাতিক কোম্পানিগুলির বহির্বিশ্বে ব্যবসা দ্বিগুণ হয়েছে, ঐ সময় আমেরিকার শ্রমিকদের গড় সাপ্তাহিক আয় কমেছে শতকরা ১৮ ভাগ, দরিদ্র আমেরিকানদের সংখ্যা বিগত ২০ বছরের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যায় পৌঁছেছে এবং ৪০ বছর আগে আমেরিকানদের আয়ের যে বৈষম্য ছিল তা আরো বেড়েছে। বেকারি, গৃহহীন মানুষের সংখ্যা ইত্যাদিও ক্রমবর্ধমান। (নিউ ইয়র্কের কাউন্সিল অব ইন্টারন্যাশন্যাল অ্যাফেয়ার্সের সভাপতি ওয়ার্ড মোরেহাউসের প্রবন্ধ, ফ্রন্টলাইন, ২১.৫-৯৩)
আমেরিকার মানুষ মানেই পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদী বা এই মানসিকতার,—তা আদৌ নয় এবং এ ব্যাপারে সামান্যতম সন্দেহ থাকার কারণ নেই। কিন্তু যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় তারা রয়েছেন, সেটির চরিত্র এই এবং আমেরিকার জনগণের বৃহদংশই তার দ্বারা তথা তার প্রতিভূ মুষ্টিমেয়ের দ্বারা শাসিত ও শোষিত। আর ব্যাপারটি এত সূক্ষ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত যে, মুষ্টিমেয় কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া আমেরিকার জনগণের বৃহদংশই এ ব্যাপারে সচেতন নয়। তাই তাঁরা ধর্মেও আছেন, জিরাফেও (অর্থাৎ বিজ্ঞানপ্ৰযুক্তির ক্ষেত্রেও) আছেন। এরই একটি প্রতিফলন ঘটে, আমেরিকার ঈশ্বরবিশ্বাস ও ধর্মপরিচয় থেকে মুক্ত ব্যক্তির স্বল্পতা থেকে, যে স্বল্পতা আমেরিকার মত জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে সবচেয়ে এগিয়ে থাকা দেশে কিছুটা স্ববিরোধী মনে হয়।(৬) আসলে তা স্ববিরোধী নয়, কারণ শুধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার নাও ঘটাতে পারে তথা ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় মৌলবাদের বিস্তার না-ও রোধ করতে পারে। এই বিজ্ঞানমনস্কতাই মানুষকে তার সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি অর্জনের ক্ষেত্রেও সাহায্য করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যান্ত্রিক ও সংকীর্ণ স্বার্থে বিকৃত ব্যবহার বিজ্ঞানমনস্কতার পরিবর্তে যান্ত্রিকতার জন্ম দেয়। বর্তমানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, আমেরিকায় প্রায় সর্বতোভাবে ও আন্তর্জাতিকভাবে নানা দেশে কম বেশি, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ তথা শাসকশ্রেণীর সেবাদাস হিসেবেই নিয়োজিত।
এর অন্য আরেকটি প্রতিফলন ঘটে, বিজ্ঞানের সাহায্যে (আসলে বিজ্ঞানের মৃত্যু ঘটিয়ে) অমানবিক হিংস্রতা প্রকাশে ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রেও। যে আধিপত্যকামী ঔদ্ধত্য আমেরিকার মত সাম্রাজ্যবাদী দেশের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, ঐ বৈশিষ্ট্য নিছক সরকারী নয়। জনমানসের বড় অংশ জুড়েই তা আছে এবং রাষ্ট্রীয় পরিচালন ব্যবস্থা এদেরই প্রতিনিধিত্ব করে। এরই একটি প্রতিফলন দেখা যায় ১৯৪৫-এ হিরোসিমা-নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমাবর্ষণ নিয়ে আমেরিকাবাসীদের মতামত সম্পর্কিত একটি সমীক্ষায়। হিটলারকে লজা দিয়ে আমেরিকা তখন এই বোমাবর্ষণের মাধ্যমে অত্যাক্স সময়ে খুন করেছিল ২ লক্ষ ২০ হাজার নির্দোষ মানুষকে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে পঙ্গু-ব্যাধিগ্রস্ত করে দিয়েছে। এই ১৯৯৫-এর জুলাই মাসে করা একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, আমেরিকাবাসীর প্রায় অর্ধেকই হিরোসিমা-নাগাসাকিতে বোমাবর্ষণকে সমর্থনা করে এবং তার জন্য আমেরিকার অনুতপ্ত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই বলেও মনে করে। বিশেষত যারা বয়স্ক তাদের মধ্যে এই বোধ আরো তীব্ৰ।(৭) প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ও আগের অধ্যায়েই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমেরিকার মৌলবাদী (ফান্ডামেন্টালিস্ট)-দের একটি বড় দাবী হচ্ছে উগ্র কমিউনিজম বিরোধী বৈদেশিক নীতির পাশাপাশি সামরিক খাতে ব্যয় বাড়ানো। সব মিলিয়ে শুধুমাত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নিছক প্রসারই ধর্মীয় মৌলবাদের সৃষ্টিকে রোধ করতে যথেষ্ট নয়। এই মৌলবাদী হিংস্ৰতারই অন্য একটি দিক সাম্রাজ্যবাদী পাশবিকতা, যা তার অস্তিত্বের স্বার্থেবিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে।
এটি তার অস্তিত্বের সংকট-অনুভবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যে অনুভব তাকে তথা তার প্রতিনিধিশ্রেণীকে ধর্মের দিকেও ঠেলে দেয়, এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে ধর্মীয় মৌলবাদ ও ধর্মান্ধতার জন্ম দিতে সক্ষম। একদা প্রগতিশীল ও বৈজ্ঞানিক চেতনাসম্পন্ন বুর্জোয়াদের এই করুণ অবনমনের প্রসঙ্গে অধ্যাপক জর্জ টমসন তার ‘An Essay on Religion’–a 335 করেছিলেন, ‘বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ইতিহাসকে বিচার করলে ধনতন্ত্রের আসন্ন ধ্বংসের বাস্তব চিত্রটিই প্রকাশিত হয়ে পড়ে এবং এই বাস্তব সত্যের মুখোমুখি হতে বুর্জেয়া চিন্তানায়কদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীকে ঘুরিয়ে ধরবার বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করে দার্শনিক ভাববাদ বা দুজ্ঞেয়বাদে আশ্রয় নেবার একটি মনোভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে!’ কিন্তু ধনতন্ত্রের আসন্ন ধ্বংসের’ বাস্তবতার কথা বল্লেও, ধনতন্ত্র এত সহজে রাস্তা ছাড়তে প্ৰস্তুত নয়। সে কৌশল পাল্টায়, চেহারায় ‘মেক আপ’ দেয়। ‘বিজ্ঞানেও অগ্রসর’ সাম্রাজ্যবাদী দেশে ধর্মের ব্যবহার, শক্তিশালীভাবে টিকে থাকা এবং ফান্ডামেন্টালিজম তথা মৌলবাদের সৃষ্টি, বিকাশ ও অস্তিত্বের পেছনে এই দিকটি গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকার মত, শিল্পবিপ্লবের সূতিকাগার ইংল্যান্ডেও একই ভাবে রাজতন্ত্রের প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় মানসিকতা এবং ধর্মের ব্যাপকতর ব্যবহার ও অস্তিত্ব বর্তমান।
অন্যদিকে পুঁজিবাদের অসম বিকাশের এলাকা এই ভারতীয় উপমহাদেশ। বুর্জেয়া বিপ্লব, শিল্প বিপ্লব, রেনেসা—কোনটিই এখানে হয় নি। চূড়ান্ত বৈষম্যের আধা সামন্ততান্ত্রিক এই দেশ বিশ্বের নানা সাম্রাজ্যবাদী ও নয়া উপনিবেশবাদী দেশের অবাধ মৃগয়াক্ষেত্র। স্বাধীনভাবে সমস্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা ও সম্পর্কের রূপান্তর ঘটিয়ে পুঁজিবাদের প্রগতিশালী ভূমিকার বিকাশ এখানে ঘটে নি। কত বিচিত্র স্বার্থের কত বিচিত্র স্তরের শ্রেণীবিভাগ থাকে। এসব দেশে। এখনকার ধর্মীয় মৌলবাদের দ্রুতশক্তিবৃদ্ধির ক্ষেত্রে এই ধরনের বিশেষ কিছু গোষ্ঠীর ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
এই ধর্মীয় মৌলবাদীদের নেতৃস্থানীয়রা অবশ্যই শাসকশ্রেণীর একটি অংশ, যে অংশ তীব্রভাবে ধর্মকে ব্যবহার করতে চাইছে এবং অপর অংশের সঙ্গে এই বিশেষ
মৌলবাদের উৎস সন্ধানে br>
স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে কিছু মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারছে। ধর্মকে এইভাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা, নিজ ধর্মীয় মাহাত্ম্য ও মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা
তাদের জঙ্গীভাবে করতে হচ্ছে।
এবং এরা উৎসাহী সঙ্গী হিসেবে পেয়েছে। পরবর্তী স্তরের অর্থাৎ মধ্যশ্রেণীর স্বচ্ছল গোষ্ঠীর পরিবারগুলিকে। বিশেষত উত্তর ভারতে বিগত দু’তিন দশকে যে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটেছে, তার ফলশ্রুতিতে উঠতি এই শ্রেণী নিজের অস্তিত্বের স্বার্থে এমন বিকল্প ধর্মীয় মৌলবাদী রাজনীতিকে সুবিধাজনক হিসেবে অনুভব করেছে। নতুন শহুরে মধ্যশ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে যারা নানা ধরনের ঋণ, ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগের উৎসাহদান ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় সত্তরের দশক থেকে সংখ্যায় অনেক বেড়েছে। গ্রামাঞ্চলেও কিছু এলাকায় সবুজ বিপ্লব (যেমন উত্তরপ্রদেশের নানা স্থানে) কিছু মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়িয়েছে। প্রকৃত বুর্জেয়া বিকাশের অভাবের কারণে, মানসিকভাবে এই শ্রেণী এখনো সামন্ততান্ত্রিক,–ধৰ্ম-পূজা আচ্চা-সতীমাহাত্ম্য ইত্যাদি তাদের মনপ্ৰাণ জুড়েই ছড়িয়ে আছে। এই অবস্থায় নেতৃস্থানীয় হিন্দু মৌলবাদীদের জঙ্গী হিন্দুত্বের প্রচার এবং মুসলমানরা তাদের আধ্যাত্মিক-অর্থনৈতিক সবদিক থেকে বিপদগ্ৰস্ত করতে পারে, এমন ভয়ের সঞ্চার করার ফলে এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি বড় অংশই হিন্দু মৌলবাদকে আত্মরক্ষার প্রধান উপায় হিসেবে গ্রহণ করেছে। ছিন্নবিচ্ছিন্ন তথাকথিত হিন্দুদের একত্রিত করতে শুধু হিন্দুত্বের প্রচার নয়, রাম মাহাত্ম্যকে সুনির্দিষ্টভাবে সামনে রাখা এবং বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে ‘রাম জন্মভূমি উদ্ধার’ (তার পরে আছে মথুরা, বেনারস ইত্যাদি ইত্যাদির শতশত ‘মন্দির’–অর্থাৎ এই উদ্ধার কর্মের দীর্ঘস্থায়ী ধারাবাহিকতার প্রচার)-এ ধরনের কর্মসূচীকেও তীব্রতার সঙ্গে হাজির করা হল। দূরদর্শনে রামায়ণের প্রদর্শন অর্থাৎ দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিভিত্তিক, অতীব সক্রিয় ধর্মপ্রচারও এ ধরনের জঙ্গী কর্মসূচীর ক্ষেত্র প্রস্তুত করায় কিছুটা সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। সমাজের একেবারে পিছিয়ে থাকা, দরিদ্রতম মেহনতী মানুষদের চেয়ে এই ধরনের মধ্যবর্তী ব্যক্তিরাই মৌলবাদের বড় সহচর। এরা কিছু সুযোগসুবিধা পেয়েছে, তাকে আরো বাড়াতে চায়, ভিন্নধর্মের মানুষদের হটিয়ে নিজেদের পথ পরিষ্কার করতে চায়। ফলে হিন্দু হিসেবে (বা বিশেষ ধর্মীয়গোষ্ঠী হিসেবে) নিজেদের অস্তিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বকে সুনিশ্চিত করার প্রশ্নের সঙ্গে এই অর্থনৈতিক নিশ্চয়তা অর্জনের লক্ষ্যও মিলেমিশে যায়।
মৌলবাদের সৃষ্টি ও টিকে থাকার পেছনে এই শ্রেণীগত অবদান বিরাট হলেও, এটিও ঠিক যে, সংখ্যায় কম হলেও, কিছু মানুষ নিছক ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে এদের দােসর হয়। কিন্তু এদের এ বিশ্বাস বিকৃত ধর্মবিশ্বাস। বিকৃত এই কারণে যে, শুদ্ধ ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্যে অন্যকে ছোট করার বা অন্য ধর্মের মানুষদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করার প্রবণতা তীব্রভাবে মোটেই থাকে না। তবু আর এস এস-বিজেপি চক্ৰ বা জামাতে ইসলামীর মত হিন্দু-মুসলিম সব মৌলবাদীদের মধ্যেই এমন হিন্দুত্ব বা ইসলামের প্রতি আনুগত্যের কারণে সচেতন বা অসচেতনভাবে তাদের খপ্পরে গিয়ে পড়া ব্যক্তির অভাব নেই। কিন্তু মৌলবাদীদের মধ্যে পাল্লা ভারী মেকী ধর্মানুগতদের দিকেই।
হিন্দুমহাসভার মত হিন্দু মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভূস্বামীদের স্বাৰ্থ রক্ষণ করা। মহাসভার সভাপতি ভি. ডি. সাভারকর তাঁর ‘হিন্দুরাষ্ট্র দর্শন’-এ ভূস্বামী ও প্রজার মধ্যে কোনো ‘স্বার্থপর’ শ্রেণীগত বিরোধের নিন্দা করেন। যুক্তপ্রদেশ থেকে পাঞ্জাব—নানা রাজ্যে মুসলিম লীগও প্রধানত নির্ভর করত। স্বধর্মের ভূস্বামীদের উপর। এইসবু সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলির দুস্বামীদের আসল লক্ষ্য ছিল ধৰ্মরক্ষার চেয়ে নিজ শ্রেণীস্বার্থ বজায় রাখা।
জামাতে ইসলামীর মধ্যেও ইসলামের প্রতি অশ্রুপাত করা লোকেদের চরিত্র এমন মেকী মুসলিমেরই। বদরুদিন উমর তার মৌলবাদের বাঙলাদেশী সংস্করণ’ প্রবন্ধে (১৬ই এপ্রিল ১৯৯২ সাপ্তাহিক খবরের কাগজ’-এ প্রথম প্রকাশিত) যেমন জানিয়েছেন, ‘এদেশে সব থেকে জনপ্রিয়া’ বলে কথিত এক অর্ধশিক্ষিত (সাধারণ শিক্ষা তো বটেই এমন কি ইসলামিয়াত এবং ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে এর কোন ধারণা নেই) জামাতী ওয়াজকর নেওয়ালা ইসলামের নামে প্রত্যেক ওয়াজের জন্য বিভিন্ন এলাকায় হাজার হাজার টাকা ফি নিয়ে থাকে। এটা তার ব্যবসা। ধর্মীয় মৌলবাদের নামে ব্যবসাদারী বাংলাদেশের ইসলামী মৌলবাদীদের একটি বৈশিষ্ট্য। সকলেই যে উপরোক্ত অর্ধশিক্ষিত মৌলভীর মত ওয়াজ করে ধন অর্জন করে তা নয়। এরা কেউ ব্যাংকের ডিরেকটর, কেউ হাসপাতালের ডিরেকটর, কেউ কোন বিদেশী পাইপ লাইনের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু যেভাবেই হোক, এদের নেতৃত্বের প্রধান অংশটিই এভাবে ইহকালে আখের গোছাতে ব্যস্ত।’
পাকিস্তানেও, জিয়াউল হকের সময় ছিল মৌলবাদী উত্থানের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাল। এই সময়ও কিছু অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছিল। কিন্তু তার মূল চরিত্রটি ছিল বিদেশী,-বিশেষত সাম্রাজ্যবাদী ও অর্থনৈতিক উপনিবেশবাদী দেশের ঋণ নিয়ে নানাভাবে তার সাহায্যে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শ্ৰীবৃদ্ধি ঘটানো। দরিদ্রদের জন্য তার কোন ভূমিকা ছিল না, বরং নেতিবাচক প্রভাবই ছিল। তাই দেখা যায় ১৯৭৭ সালে পাকিস্তানের গ্রামে দারিদ্র্য সীমার নীচের মানুষ ছিল শতকরা ৩৫ ভাগ, ১৯৭৯-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় শতকরা ৩৭ ভাগ। জিয়া-অৰ্থনীতির সামগ্রিক চরিত্রের আঁচ এ থেকে পাওয়া যায়। আর এই অবস্থায় একদিকে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ দরিদ্র জনসাধারণকে ভুলিয়ে রাখতে ধর্মের আফিম গেলাবে এবং অন্যদিকে নিজেরাও ধর্মকে আঁকড়ে রাখবে (অর্থাৎ ধর্মানুসরণের ভান করবে)-এতে অস্বাভাবিকত্ব হয়তো বিশেষ কিছু নেই। হিন্দু বিরোধিতা, বাঙলাদেশ বিরোধিতা (এবং বাঙলাদেশের মুসলিমরা প্রকৃত মুসলিম নয়—এমন প্রচার) ইত্যাদিও এই কারণেই করতে হয়।
আখের গোছানোর ধান্দায় ব্যস্ত মানুষেরা মৌলবাদীদের পুষ্টি জোগানো, এমনকি উত্থান ও সৃষ্টির ক্ষেত্রে সাহায্য করলেও, শুধু এটিই মৌলবাদ সৃষ্টির প্রধান দিক নয়। আগেই বলা হয়েছে, ধর্মের প্রতি বিশ্বাস, ধর্মান্ধতা, আপন অস্তিত্বের সঙ্গে ধর্মপরিচয়কে একাত্ম করে তোলা এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, মতাদর্শ বা ভিন্ন ধর্মের দ্বারা এই ধর্মের তথা আপন অস্তিত্বের বিপন্নতাবোধের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি যেমন এই সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে, তেমনি বিশেষ শ্রেণীর আধিপত্যকামী, নেতৃত্ব লোভী, অর্থনৈতিক সুবিধাবাদী মানসিকতাও এই সৃষ্টিকে ত্বরান্বিত করে। কিন্তু এটিও সব নয়। ধর্মীয় মৌলবাদ সৃষ্টির পেছনে আরেকটি বড় ভূমিকা পালন করে, জনসাধারণের সামনে উপযুক্তভাবে সংগঠিত সঠিক দিশার শূন্যতাও।
এই দিশাকে মার্কসীয় দর্শন অনুসারী হতেই হবে তার কোন মানে নেই। প্রকৃতই ধর্মনিরপেক্ষ উদার মতাদর্শও যদি সংগঠিতভাবে জনগণের নেতৃত্ব দিতে ও তাদের সমস্যার সমাধানে নিজের আন্তরিক ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তাদের আস্থা অর্জন করতে ও জনগণের বৃহদংশের মধ্যে বৈজ্ঞানিক, ধর্মনিরপেক্ষ, উদার, মানবতাবাদী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে পারে (অন্তত তাদের সামনে তা রাখতে পারে), তাহলে মৌলবাদের সৃষ্টি ও বিস্তার ব্যাহত হতে বাধ্য। যখনই যেখানে এই শূন্যতা থাকে তখন, অন্যান্য শর্তসাপেক্ষে, ধর্মীয় মৌলবাদ এই শূন্যতা পূরণ করতে এবং জনগণের হতাশার সমাধান করার অভিনয় করে তাদের বন্ধু হতে এগিয়ে আসে। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে ধর্মকে এমন মৌলবাদী জঙ্গীপনা করতে হচ্ছে, কারণ আধুনিক বিশ্বে তথাকথিত ঐসব প্রতিষ্ঠানিক ধর্মের অস্তিত্ব যে বিপন্ন তা অনুভব করা যাচ্ছে(৮), ফলত তার প্রতিক্রিয়ায় ধর্মের মূল বা শিকড়ে ফিরে যাওয়ার তাগিদটিকে অর্থনৈতিক শ্রেণী স্বার্থের সঙ্গে মেলাতে হচ্ছে। (কারণ এখনকার প্রধান অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও সংকটের মুখে নিজেকে বাঁচাতে গ্যাট চুক্তি থেকে হাজারো কৌশল নিতে বাধ্য হচ্ছে। তবু দেশের মানুষের বেকারত্ব, ক্রমবর্ধমান বৈষম্য, ক্রম হ্রাসমান মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও মাথাপিছু আয়, এগুলি রোধ করা যাচ্ছে না।)
মৌলবাদ এইভাবে হতাশা ও নেতিবাচক অবস্থার ফসল। অলৌকিক শক্তির কল্পনা মানুষের আদিম বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। অন্যান্য প্রাণী বা জীবজন্তু থেকে যে সব দিক মানুষকে গুণগতভাবে পৃথক করেছে, এটি তার অন্যতম। ধর্মের ও তার অনুশাসন-মূল্যবোধের সংকলন মানুষের মানবিক ইতিবাচক দিকেরই প্রকাশ, যদিও ক্রমশ তার শ্রেণী স্বার্থে ব্যবহারও ঘটেছে। কিন্তু নিজের সমাজ ও গোষ্ঠীকে সুশৃঙ্খলভাবে ধরে রাখার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা পশুদের গোষ্ঠী থেকে মানুষের সমাজকে আলাদা করে। এবং এর ফলেই মানুষ পরিবর্তিত পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী তার চিন্তাভাবনা, সমাজ-অৰ্থনীতি তথা ধর্মেরও পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কিন্তু যখন এই পরিবর্তনকে অস্বীকার করা হয় এবং ধর্মের নাম করে মানুষে মানুষে চূড়ান্ত বৈরিতামূলক বিভেদ, পারস্পরিক ঘূণা ও ব্যাপক জনগণকে প্রতারণা করার মাধ্যমের সৃষ্টি করা হয়, তখন আর তা মানবিক ও ইতিবাচক থাকে না। তখন আর ধর্ম মানুষকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রাচীন তথা অন্তত তৎকালে প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করে না। বর্তমান পৃথিবীতে নতুন জ্ঞানের আলোয় ঈশ্বর বিশ্বাসের তথা ধর্ম বিশ্বাসের বৈপ্লবিক পরিমার্জনার প্রয়োজনও স্পষ্ট অনুভব করা যাচ্ছে। এ অবস্থাতেও ধর্ম যদি রাস্তা না ছেড়ে দেয় এবং ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদী ক্রিয়াকাণ্ডের মাধ্যমে নিজেকে টিকিয়ে রাখার প্রচেষ্টার পাশাপাশি মানুষের মনুষ্যত্ব ও আর্থসামাজিক বিকাশকে আচ্ছন্ন করতে থাকে, তবে এই ক্রিয়াকাণ্ডের উচ্ছেদ করাটাই অন্যতম প্রাথমিক দায়িত্ব।
কিন্তু এই দায়িত্ব যাদের করার কথা বা যাঁরা করবেন বলে প্ৰতিশ্রুতি দেন, তারা যদি সংগঠিত না হন এবং দায়িত্বপালনের ক্ষেত্রেও যদি ফাঁকি থাকে, তবে ঐ শূন্যতার সুযোগে ধর্মান্ধতা, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ মাথা তুলে চাড়া দেবেই। বাস্তবত দেখা গেছে। যখন জনগণকে নিয়ে সুস্থ সামাজিক সংগ্রাম পরিচালিত হয় ও তার জোয়ার আসে, তখন সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তিগুলো পিছু হঠতে বাধ্য হয়। কয়েক দশক আগে এই বাংলায় ব্যাপক বামপন্থী আন্দোলন ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদী জাতীয়তাবাদের প্রসার-প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। সত্তরের দশকের তথাকথিত নক্সাল আন্দোলনের সময়ও সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান আদৌ লক্ষণীয় ছিল না। কিন্তু সারা ভারতব্যাপী এই বৈপ্লবিক আন্দোলন (তার সমস্ত ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও)। যখন এক সময় ব্যর্থ হল এবং মানুষকে হতাশ করল, তখন নানা গুরুবাবা-মাতাজিদের জঙ্গী আবির্ভাব নতুন করে ব্যাপকভাবে ঘটতে শুরু করল। ধর্মকে কিছু মানুষও আঁকড়ে ধরল শান্তি ও মুক্তির উপায় হিসাবে। এমন কি সংখ্যায় নগণ্য হলেও এমন লড়াকু নক্সাল’ কর্মীদের কেউ কেউ বিজেপি-র মত মৌলবাদী সংগঠনে যুক্ত হয়েছে—এমন উদাহরণও রয়েছে এবং ধাৰ্মিক কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে গেছে এমন উদাহরণ তো আছেই।
আরো আগে ভারতে যখন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জোয়ার এসেছে তখনও এই সব ধর্মীয় অপশক্তি মাথা চাড়া দিতে পারে নি। ‘১৯১৮ থেকে ১৯২২ পর্যন্ত বছরগুলি ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রাম ও হিন্দু মুসলিম ঐক্য, উভয়েরই সুখকর সময়। ১৯২৬-এর পর বামপন্থার উত্থান, ট্রেড ইউনিয়নদের এবং যুব আন্দোলনের বৃদ্ধি এবং সাইমন কমিশন বিরোধী প্রতিবাদ আন্দোলন আবার জনগণকে উদ্দীপিত করে এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা কমিয়ে দেয়। ১৯৩০-৩৪-এ আইন অমান্য আন্দোলন গোটা দেশে ঝড় বইয়ে দেয়। হিন্দু ও মুসলিম সকলেই ব্যাপক সংখ্যায়। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। সাম্প্রদায়িক দলগুলি ও নেতারা হয়। কার্যত অবসর গ্ৰহণ করেন অথবা ইতস্ততভাবে জাতীয় আন্দোলনকে সমর্থন করেন।. ১৯২০-র দশকের শেষে ও ১৯৩০-এর দশকে ক্রমবর্ধমানভাবে হিন্দু, শিখ ও মুসলিম যুবক ও শ্রমিকরা এবং অনেক এলাকায় কৃষকরা, রাজনৈতিক নেতৃত্বের জন্য তাকাচ্ছিলেন কমিউনিস্টদের, সমাজতন্ত্রীদের, নওজয়ান ভারত সভার, বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের এবং নেহরু ও সুভাষচন্দ্ৰ বসুর দিকে। মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, আর.এস.এস. এবং অন্যান্য সাম্প্রদায়িক সংগঠনের প্রভাব ছিল নূ্যনতম।’ (বিপিনচন্দ্ৰ)
এই ভাবেই ধর্মীয় প্রভাবমুক্ত বা ধর্মনিরপেক্ষ বৈপ্লবিক আন্দোলন যেমন সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদের উত্থানে বাধা দেয়, তেমনি তাদের অভাবও তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।
পৃথিবী জুড়েই বামপন্থী আন্দোলনের দুর্বলতা ও নানা ধরনের ভাঙ্গন, বিভ্রান্তি যেমন এখন জনমানসে কোন বিকল্প আশা জাগানোর ক্ষেত্রে ব্যর্থ হচ্ছে। আন্তর্জাতিকভাবে মৌলবাদের উত্থানে এটিও বড় ভূমিকা পালন করছে। প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, মুক্তমনা ব্যক্তিরাও সংগঠিত লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ নন। এ অবস্থায় সামাজিক-অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্রে জনগণের হতাশা ঈশ্বর ও ধর্মকে আঁকড়ে রাখার তথা সাম্প্রদায়িক মৌলবাদীদের খপ্পরে পড়ার পরিবেশ সৃষ্টি করে।
আর তথাকথিত বামপন্থীরা বা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মত তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিরা যখন সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে ও সাময়িক সমস্যাকে এড়ানোর জন্য ধর্মীয়, এমনকি ধর্মীয় মৌলবাদী অপশক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হয়, তাদের সহযোগী সংগ্ৰামী হিসাবে গ্ৰহণ করে এবং প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে তাদের রাজনৈতিক-সামাজিক প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে, তখন জনসাধারণের সামনে আরো জটিল বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং এই সব অপশক্তির গ্রহণযোগ্যতাও বাড়ে। এমনকি ধর্মীয় মৌলবাদীসাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার কথা যাঁরা বলেন (যেমন ভারতে বামপন্থীরা ও কংগ্রেসীরা) তাঁরাও ঐক্যবদ্ধ নন। ছুৎমার্গ ত্যাগ করে অন্তত এই বিষয়ে যুক্তফ্রন্ট ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এরা পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়ে, আবার নয়া ফ্যাসিস্ট ঐ ধর্মীয় অপশক্তিগুলির বিরুদ্ধেও লড়ে। ফলে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইটিও যেমন দুর্বল হয়, তেমনি তাদের আসল শত্রু কে তা নিয়েও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়।
এই বিভ্রান্তি আরো বাড়ে যখন দেখা যায় তথাকথিত বামপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিরা শুধু দলগতভাবে ধর্মীয় অপশক্তির সঙ্গে আঁতাত গড়ার উদাহরণ সৃষ্টি করা নয়, ব্যক্তিগতভাবেও ধর্ম ও ধর্মাচরণকে অনুসরণ করেন। মুখে মার্কসীয় দর্শনের কথা বলেও এবং বামপন্থী দলের কমী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেও, যখন নেতৃস্থানীয় বা বিরল দু’ চারজন বাদে, বাকী সবাই পূজাআচ্চায় অংশগ্রহণ করা বা উৎসাহ দেওয়ার সঙ্গে, শ্ৰাদ্ধ-’শুভ’ বিবাহ-উপনয়ন-পৈতে-কোরান খানিনামাজ জাতীয় নানাবিধ ব্যক্তিগত ক্রিয়াকাণ্ডে নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মানুষ্ঠান করেন (অন্তত তার সক্রিয় প্রতিবাদ করেন না, বরং সমর্থনে নানা যুক্তি দেখান) এবং নিজের প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম পরিচয়কেও দূর করেন না, তখন অন্য মানুষ এদের বস্তুবাদী দর্শন ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে খুব একটা আমল যে দেবেন না তাতে কোন সন্দেহ নেই। পাশাপাশি দেখা যায়, যে ব্যক্তিত্বের উদাহরণ লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করতে পারত, পশ্চিমবঙ্গের সেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, তার অতীত সংগ্রাম ও বিচক্ষণ নেতৃত্ব সত্ত্বেও, ডঃ পাচু গোপাল রায়ের ভাষায়, ‘রিলিজিয়াস ওয়াইফ’ ও ‘ক্যাপিট্যালিস্ট সন’-কে সপ্ৰেমে-সস্নেহে মদত দিয়ে যান। অবশ্যই তাঁর সহকমী নেতৃত্বের অনেকেই এই ধাৰ্মিকতা ও পুঁজিলোভী মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন। কিন্তু কারোর ব্যক্তিগত আচরণ ও বিশ্বাসে আঘাত না করার নাম করে, সর্বোচ্চ নেতৃত্বের এমন দু একজনের এবং তার ঘনিষ্ঠতমদের মধ্যেও এমন আচরণ ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে লড়াই না করাটা বামপন্থার অন্তঃসারশূন্যতার দিকে ইঙ্গিত করতে যথেষ্ট। এ অবস্থায় ধর্মের জনবিরোধী অপব্যবহারের বিরুদ্ধে এবং ভাববাদী দর্শনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করা তথা বস্তুবাদী দর্শনে অন্যদের শিক্ষিত করার কাজের ভিত্তিটিই আলগা হয়ে যায়। বামপন্থীদের এমন রিলিজিয়াস ওয়াইফ’-রা মৌলবাদী নিশ্চয়ই নন, হয়তো হবেনও না, কিন্তু তা সাধারণ মানুষকে রিলিজিয়াস’ না হওয়ায় অনুপ্রাণিত অন্তত করে না। এবং এরা যদি ধর্মান্ধতা-সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদী শক্তির শিকার হন তবেও অবাক হওয়ার কিছু নেই।
পশ্চিমবঙ্গের প্রসঙ্গে বলা যায়, সংগঠিত বামপন্থী দলের এহেন উদাহরণ এবং অন্যান্য বামপন্থীদের অসংগঠিত অবস্থানের সঙ্গে, প্রায় দু দশক ধরে তথাকথিত বাম-শাসনের পরেও এখানকার জনগণের নানা সমস্যার এমন কিছু গুণগত কোন পরিবর্তন ঘটে নি, বরং বাড়ছে। ব্যাপারটি অবশ্যই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা জটিলতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বিচ্ছিন্নভাবে একটি দেশের একটি রাজ্যে জনগণের সব সমস্যার সমাধান ঘটে যাবে, এটি ভাবাটাও হাস্যকর। কিন্তু সমস্ত কয়েমী স্বার্থগুলিকে প্ৰতিহত করে জনগণকে সংগঠিত করার এবং সংগঠনের সর্বস্তরে বস্তুবাদী দার্শনিক প্রচারের কাজও নিতান্তই অবহেলিত, অন্তত সংগঠন বাড়ানো ও ভোট কুড়ানোর উদ্যোগের তুলনায়। এ অবস্থার একটি ভয়াবহ পরিণতি হল, বিজেপি-র মত ধর্মীয় মৌলবাদীদের পশ্চিমবঙ্গের মত ‘বামপন্থী’, ‘আলোকিত রাজ্যেরও তৃণমূল অব্দি সংগঠনের বিস্তার ঘটাতে সক্ষম হওয়া-তা সে যত দুর্বল ভাবেই হোক না কেন। এই বিস্তারকে উপেক্ষা করার ভবিষ্যৎ পরিণাম ভয়াবহ হতে বাধ্য।
ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ প্রতিরোধে বামপন্থা ও বামপন্থীদের কাছে প্রত্যাশা অনেক বেশি বলেই ব্যাপারটি বেশি নাড়া দেয়। ভারতের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক সংগঠন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সহ অন্যান্য দক্ষিণপন্থীদের থেকে এ প্রত্যাশা অনেক কম, তার বড় কারণ তারা বস্তুবাদী দর্শনের কথাই বলে না, এবং ভাববাদের বিরুদ্ধে লড়াইটিও তাদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত নয়। তবু ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলেও এই দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বকে দেখা যায় সাইবাবার মত ম্যাজিসিয়ানধর্মব্যবসায়ীদের বা চন্দ্ৰস্বামীর মত ধান্দাবাজ ধৰ্মজীবীদের পেছনে পেছনে ঘুরতে, মন্দির-মসজিদ-গীর্জার ঐশ্বরিক শক্তির কাছে নতজানু হতে, যজ্ঞ ও জ্যোতিষসহ নানা অপবৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকাণ্ডের সাহায্য নিতে। এমনকি আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কথা বলা প্ৰয়াত রাজীব গান্ধীও তার ব্যতিক্রম ছিলেন না। এদের কেউ এসব করেন নিজস্ব বিশ্বাস থেকে, কেউ বা ভোটের বাক্সের দিকে তাকিয়ে। আর জাতপাতের রাজনীতি তো বাম-ডান সব রাজনৈতিক দলেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। ধর্ম ও জাতপাতের অস্তিত্ব সমাজে আছে বলেই রাজনীতিতে তা প্রতিফলিত হয়। কিন্তু তা অবশ্যম্ভাবী। নয়। সচেতন শুভ ইচ্ছায় ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিও করা সম্ভব এবং তাইই কাম্য, তাইই সুস্থ। আসলে অৰ্জ্জুন যেমন জলে মাছের ছায়া দেখে মাছকে বাণবিদ্ধ করে দ্ৰৌপদীকে লাভ করেছিলেন, এইসব ক্ষমতালিঙ্গু রাজনৈতিক দলগুলিও ভোটারদের ধর্মবিশ্বাসের দিকে লক্ষ্য রেখে ধর্মের বাণে তাদের হৃদয়বিদ্ধ করার চেষ্টা করেন। এবং লাভ করতে চান আকাঙ্খিত গদিটি।
এইসব রাজনৈতিক দলগুলির কাজের পদ্ধতিতেও ধর্মীয় মৌলবাদীদের মত রাজনৈতিক সংকীর্ণতার আভাষ পাওয়া যায়। এতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা সাধারণ মানুষ ধর্মীয় মৌলবাদীদের কথাবার্তাতেও খুব একটা অস্বাভাবিকত্ব খুঁজে পায় না। সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় মৌলবাদ যেমন মানুষের মানুষ পরিচয়ের চেয়ে ধর্মীয় বা সম্প্রদায়গত পরিচয়কেই প্রধান বলে গণ্য করে, উগ্র-অনুগ্র ‘কম্যুনিষ্ট’ বা কংগ্রেসসহ নানা রাজনৈতিক দলও একই ভাবে মানুষের মানুষ পরিচয় ভুলিয়ে দিয়ে কে কোন পার্টি করে বা কোন পার্টির কাছাকাছি-এইটিকেই প্রধান বিবেচ্য বলে মনে করে। শত্ৰু-মিত্ৰ চেনা বা শ্রেণীবিভাজন করা অবশ্যই দরকার, কিন্তু যখন তার নাম করে ভিন্ন রাজনৈতিক দলের দরিদ্র এক ছাপোষা মানুষ বা কৃষক-শ্রমিককেও শত্রুর পর্যায়ে ফেলে দেওয়া হয় কিংবা হত দরিদ্র এক কনস্টেবল ট্রাফিক পুলিশকে শ্রেণীশত্রু হিসেবে গণ্য করে হত্যা করা হয় (এবং বিরাট বৈপ্লবিক কাজ করা হল বলে তৃপ্ত হওয়া যায়), তখন তার সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদের সংকীর্ণতার খুব একটা তফাৎ পাওয়া যায় না।
ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদীরা যেমন আপনি সম্প্রদায়ের বা ধর্মের সবার স্বার্থ সমান করে দেয় (অন্তত প্রচারের ক্ষেত্রে) এবং ভিন্ন সম্প্রদায় বা ধর্মের সবাইকে শত্রুর পর্যায়ে ফেলে দেয়, এই রাজনৈতিক দলবাজাদের বৃহদংশও তাই করে। ভিন্ন রাজনৈতিক দলের উপযুক্ত দাবিগুলিও তাদের কাছে মর্যাদা পায় না। ধর্মের নাম করে মানুষে মানুষে যখন এই অসুস্থ বিভেদ সৃষ্টি হয়, তখন বুদ্ধ-মহাবীরচৈতন্য-নানক বা রামকৃষ্ণের মত বহু ধর্মীয় নেতাই মানবিক সৌভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। একইভাবে মার্কস বা গান্ধীর মত রাজনৈতিক মতাদর্শের বহু প্ৰবক্তাও কখনো এটি বলেন না যে, তাকে কেন্দ্র করে একটি সংকীর্ণ গোষ্ঠীবদ্ধতার সৃষ্টি হোক। তবু ধর্ম এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের এমন বিকৃত ব্যবহার ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক মৌলবাদীরা করে যায়। ধর্মীয় মৌলবাদীরা ধর্মের বিতর্কিত সুবিধাজনক মূল দিকগুলিকে সময়োপযোগী না হলেও আপনি শ্রেণীস্বার্থে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। রাজনৈতিক মৌলবাদীরাও একইভাবে তাদের রাজনৈতিক মতাদর্শকে সময়ের সঙ্গে পরিমার্জিত না করে হুবহু প্রয়োগ করে চলে এবং তার থেকে খুঁটিনাটি বিচ্যুতিতে গেল গেল’ রব তোলে। ধর্মীয় মৌলবাদীরা রাম বা কৃষ্ণের মত এক একটি চরিত্রকে বেছে নিয়ে অন্ধভাবে তার মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠায় নামে, রাজনৈতিক মৌলবাদীরাও মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-স্টালিন-মাওসেতুং (-শিবদাস ঘোষ)-মহাত্মা গান্ধী (ইন্দিরা গান্ধী-রাজীব গান্ধী)-দের প্রতি অন্ধ ব্যক্তিপূজা শুরু করে। এদের কোন ধরনের সমালোচনাকেই প্রতিক্রিয়াশীলতা বা সম্পূর্ণ ভিন্ন। মেরুর অন্তর্ভুক্ত বলে ছাপ মেরে দেওয়া হয়। একইভাবে ধর্মীয় মৌলবাদী-সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিরাও ধর্মের খুঁটিনাটি বিচ্যুতিতেই ‘ধম বিপন্ন’ বলে আওয়াজ তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাই মসজিদের সামনে শুয়োর মেরে রেখে এই ধরনের মুসলিমদের ক্ষেপিয়ে দেওয়া যায়(৯) আর মহরমের মিছিলে এই ধরনের হিন্দুদের গা কসকস করতে থাকে। রাজনৈতিক দলবাজি করতে করতে এই ধরনের অমানবিক বিভেদ সৃষ্টি, বৈরিতা, সংকীর্ণতা ইত্যাদির চর্চা যখন চলে তখন ধর্মীয় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা একই কর্মপদ্ধতি চালিয়ে খুব একটা নিন্দাৰ্থ হয়ে ওঠে না। সরল ধর্মবিশ্বাসী মানুষ দেখে ধর্মীয় এইসব লোকেরা অন্তত তার ধর্মবিশ্বাসকে মর্যাদা’ দেয়, ধর্মীয় গোষ্ঠীর স্বাৰ্থ রক্ষায় ‘প্ৰাণপাত’ করে। ঐসব শ্রেণীভিত্তি, অর্থনৈতিক বিচার-বিশ্লেষণের মত বড়বড় বিচারের চেয়ে কাজকর্ম ও মানসিকতার এই বাহ্যিক সাদৃশ্যও অনেক মানুষকে রাজনৈতিক মৌলবাদীদের কোল থেকে ধর্মীয় মৌলবাদীদের কোলে ঠেলে দেয় এবং ধর্মীয় মৌলবাদীদের গ্রহণীয় করে তোলে।
সংকটাপন্ন অস্তিত্বের অনুভব ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। এই সংকট নতুন মতাদর্শের কারণে হতে পারে—আমেরিকায় যেমন ফান্ডামেন্টালিজম-এর সৃষ্টি হয়েছিল প্রাথমিকভাবে খৃস্টের অভ্যুত্থান জাতীয় ধর্মীয় কুসংস্কারাচ্ছন্ন মিলেনারিয়ান আন্দোলনের স্তর পেরিয়ে বিবর্তনবাদ ও কম্যুনিজমকে ধর্মের অস্তিত্ব বিপন্নকারী হিসেবে অনুভব করে। এই মতাদর্শগত বিপন্নতার প্রতিফলন ঘটে সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও যখন সামন্তশ্রেণী এবং বিশেষত বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের শ্রেণীগত সংকট অনুভব করতে থাকে। তাই ফরাসী বিপ্লবের আগে যে প্রগতিশীল বুর্জেয়ারা ধর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল, তারাই পরে ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে। হিন্দু ও ইসলামী মৌলবাদীদের ক্ষেত্রেও এটি কম বেশি সত্য। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান যতই ধর্মকে কোণঠাসা করতে থাকে, ততই এরা মরিয়া হয়ে ওঠে। হিন্দু মৌলবাদীরা তাই কয়েক সহস্র বছরের পুরনো রামমাহাত্ম্যকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে চায়, বৈদিক শিক্ষাকে ফিরিয়ে আনতে চায়। মুসলিম মৌলবাদীরা ধর্মভিত্তিক মাদ্রাসা শিক্ষাকে জোরদার করে, হাজার দেড়েক বছরের পুরনো কোরান ও হাদিসকে হুবহু অনুসরণ করতে চায়।
সব মিলিয়ে ধর্মীয় মৌলবাদের সৃষ্টি, টিকে থাকা ও পরিপুষ্টির জন্য কয়েকটি শর্তের কথা উল্লেখ করা যায়
(১) প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রতিকুল শক্তির কাছে মানুষের অসহায়তা এবং অসম্পূর্ণ জ্ঞান,
(২) যে ব্যবস্থার উপরিকাঠামো হিসেবে ধর্ম ও ঈশ্বরবিশ্বাস টিকে থাকে ঐ ব্যবস্থার অস্তিত্ব,
(৩) ধর্মের ভিত্তিকে চ্যালেঞ্জ করার মত বৈজ্ঞানিক তথ্য, চিস্তা ও আদর্শএর উদ্ভব, এবং তার প্রতি প্রতিক্রিয়া,
(৪) শাসকশ্রেণীর বিশেষ অংশের বিপন্নতাবোধ, এবং তাদের মধ্যে এই বিপন্নতা কাটানোর জন্য নিজেদের ও নিজেদের অধীনে অন্যদের সংগঠিত করতে ধর্মকে ব্যবহার করার প্রবণতা,
(৫) চারপাশে সুবিধাভোগী ধর্মবিশ্বাসী মধ্যশ্রেণীর অস্তিত্ব এবং তাদেরও নিজ স্বার্থের ও অস্তিত্বের সংকট,
(৬) ধর্মবিশ্বাসী বিপুল সংখ্যক সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ, যাদের বিভ্রান্ত করা যায় ও যারা নিজ ধর্মের স্বার্থে বিভ্রান্ত হতে প্ৰস্তুত এবং দীর্ঘকালীন সমস্যার কারণে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হওয়া হতাশা,
(৭) বৈজ্ঞানিক, ধর্মনিরপেক্ষ কিংবা গণমুখী বামপন্থী আন্দোলনের অভাব বা দুর্বলতা,
(৮) জনগণের বৃহদংশের সচেতনতা সৃষ্টি করা, আস্থা অর্জন করা ও সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষ-বামপন্থীদের ব্যর্থতা,
(৯) ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ধর্মান্ধতা-সাম্প্রদায়িক-মৌলবাদী শক্তির অস্তিত্ব ও প্ররোচনা এবং তাদের দ্বারা নিজেদের সামাজিক-অৰ্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে বলে বিশ্বাসের সৃষ্টি হওয়া,
(১০) জনগণের বৃহদংশের সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক তথা সুস্থ জীবন যাপনের নানা সমস্যাবলীর সমাধানে অক্ষম এবং বৈষম্যভিত্তিক, শোষণজীবী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে আগ্রহী শাসকশ্রেণীর দ্বারা, জনগণের ধর্মবিশ্বাসকে ব্যবহার করে। তাদের বিভ্রান্ত করার জন্য তথা আত্মরক্ষার জন্য ষড়যন্ত্রমূলক কৌশল।
শাসকশ্রেণীর একাংশের এই ষড়যন্ত্রমূলক কৌশলই ধর্মীয় মৌলবাদের জন্ম দেয়। মানুষের হতাশা আর যুক্তিহীন ধর্মীয় আবেগ ও বিশ্বাস তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখে। বিকল্প বৈজ্ঞানিক মতাদর্শের অভাব বা ব্যর্থতা তার জন্য স্থান ছেড়ে দেয়। এই মৌলবাদ মানুষের সংগ্রামকে বিপথগামী করে। সংগ্রামী মানুষদের ধর্মের নামে বিভক্ত ও দুর্বল করে দিতে এবং মূল শত্রুর পরিবর্তে পরস্পরের মধ্যে হানাহানি করে শক্তিক্ষয় করতে প্ররোচিত করে। সমাজ ও তার সমস্যা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক উপলব্ধি অর্জনে বাধা দেয়। মন ও চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে অলীক ও কল্পিত ঈশ্বরে বিশ্বাসের দ্বারা এবং এই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানিক ধর্মে মোহের দ্বারা। বৈজ্ঞানিক মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে ও মানুষকে ভালবাসতে বাধা দেয়। এইভাবেই মৌলবাদ তার অবৈজ্ঞানিক, অমানবিক, প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র নিয়ে গণশত্রুদের অভিষেকের আয়োজন করে।
ধৰ্মীয় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা সচেতনভাবে সৃষ্টি করা একটি মানসিকতা তথা বিশেষ ধরনের আন্দোলনের প্রক্রিয়া। ঐশ্বরিক অলৌকিক শক্তির ও আত্মা জাতীয় কোন একটি কিছুর কল্পনা ও বিশ্বাস, অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নানা বিধিনিষেধ ও সংস্কারের সৃষ্টি ইত্যাদির মত মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা জনগণের মধ্যে প্রায় সর্বজনীনভাবে ও স্বতঃস্ফুর্তভাবে সৃষ্টি হয় না। তাকে সক্রিয় উদ্যোগে সৃষ্টি করা হয়। সৃষ্টি করে স্বল্পসংখ্যক কায়েমী স্বার্থের সংকীর্ণ চিন্তার কিছু মানুষ। তারা তাকে ছড়িয়ে দেয় জনগণের মধ্যে। অবৈজ্ঞানিক মানসিকতা, যুক্তিহীন আবেগ, সুস্থ বিকল্পের অভাব, নিজস্ব হতাশা ও নানাধরনের বিভ্রান্তির কারণে জনগণের একাংশ তাকেই নিজের মুক্তির পথ ভেবে বসে। এই ভাবনা তাকে যখন সর্বনাশের দোরগোঁড়ায় দাঁড় করায়, তখন সে দেখে সে নিজের ভাইকে হত্যা করেছে, প্রতিবেশী বন্ধুকে পর করে দিয়েছে, সে নিজে আটকেছে আরো শক্তিশালী বাঁধনে। আর দেখে, ঐ দোর গোঁড়ার বহু দূরে সব মৌলবাদীরা পরস্পরের কঁধে হাত দিয়ে এই বাঁধন হাতে হাসি মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।
——————
(১)এই যুক্তিবোধহীন অবৈজ্ঞানিক অন্ধবিশ্বাস হচ্ছে ধর্মান্ধতাত তথা ধর্মীয় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী মানসিকতার সৃষ্টি ও টিকে থাকার একটি বড় ভিত্তি। ১৯৯৫ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর একেই মূলধন করে ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা সম্ভবত তাদের পরিকল্পিত এক ভয়াবহ ভবিষ্যৎ ষড়যন্ত্রের রিহার্সেল করে; সারা ভারতে ও ভারতের বাইরেও তারা সুকৌশলে রটিয়ে দেয় যে, গণেশ মূর্তি (এবং শিব, দুৰ্গা ইত্যাদির মূর্তিও) ভক্তদের দেওয়া দুধ পান করছে। লক্ষ লক্ষ সরল ধর্মবিশ্বাসী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ এর ফলে দলে দলে বাড়িতে বা মন্দিরে ঐ সব মূর্তিকে দুধ খাওয়াতে থাকে এবং সারা ভারত জুড়ে আচমকা এক গণউন্মাদনার সৃষ্টি হয়। আমেরিকা-ইংল্যাণ্ডের মন্দিরেও তার খামতি ছিল না। ব্যাপারটি যে সুপরিকল্পিতভাবে প্রচারিত একটি গুজব ও রটনা, তা বোঝার জন্য শুধু এটি বোঝাই যথেষ্ট যে, অতি অল্প সময়ে এমন গুজব ছড়িয়েছে প্রধানত শহরাঞ্চলে যেখানে এস টি ডি করে টেলিফোনে এমন গুজব ছড়ানো গেছে বা গুজব ছড়ানোর নির্দেশ দেওয়া গেছে। গ্রামের লোকেরা বেশি কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলে ধারণা থাকলেও, সেখানে এই উন্মাদনা ছড়ায়নি। গণেশের গুড়ই হোক বা ছাগলমূর্তির পা-ই হোক,-দুধ, মদ, সাবান জুলি, কেরোসিন তেল ইত্যাদি, তরলের পৃষ্ঠটান (surface tension) & Kirrtt isfits first (Capiliary action)-এর জন্য এই তরলসহ চামচ ওখানে ঠেকালে সেটি আস্তে আস্তে বেয়ে যায়। এতে অলৌকিকতার কোন ব্যাপার নেই। কিন্তু বিশ্বহিন্দু পরিষদ সহ নানা হিন্দুত্ববাদী ও হিন্দুমৌলবাদী গোষ্ঠীই এটিকে দৈবী ব্যাপার বলে এবং আগামী শতাব্দী যে ‘হিন্দু শতাব্দী’ হতে যাচ্ছে তার লক্ষণ বলে অভিহিত করেছে। (এশিয়ান এজ, আনন্দবাজার পত্রিকা ইত্যাদি; ২২৯.৯৫) সব দেখে শুনে মনে হয় ব্যাপারটি মৌলবাদীদের একটি সুপরিকল্পিত কর্মসূচীর অঙ্গ। কত তাড়াতাড়ি তারা দেশ জুড়ে যুক্তিবোধহীন ও ধর্মবিশ্বাসী অসংখ্য মানুষকে (হিন্দুদের) উন্মত্ত করে তুলতে পারে,-যথাসম্ভব তা যাচাই করার জন্যই গণ উন্মাদনার সৃষ্টি।
এইভাবে ভবিষ্যতে কোন একদিন যদি তারা হঠাৎ দেশজুড়ে রটিয়ে দেয় যে, মথুরা বা অযোধ্যায় কয়েক শত হিন্দুকে মুসলমানরা মেরে ফেলেছে (এবং তা জোরদার করতে কিছু দরিদ্র বস্তিবাসী হিন্দুকে তারা মেরেও ফেলতে পারে) তবে ভয়াবহ মুসলিম নিধন ও তার প্রতিক্রিয়ায় উন্মত্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানো সম্ভব হবে। ২১শে সেপ্টেম্বর যারা দুধ ভরা চামচ নিয়ে গণেশ মূর্তির দিকে ছুটেছিল, তারাই তখন কোন যুক্ত বা তথ্যের ধারে কাছে না গিয়ে, কোনকিছু তলিয়ে না দেখে, ছুরি হাতে প্রতিবেশী মুসলিমদেৱ দিকে ছুটে যাবে। সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হিন্দুমৌলবাদীদের পরিকল্পিত জঙ্গী লড়াই-এর রিহার্সেল হল না তো ঐ গণেশের দুধ খাওয়ার গণ উন্মাদনার সৃষ্টি?
(২) বিবর্তনবাদ’ কথাটি এখানে একটি পৃথক তত্ত্ব হিসেবে তো বটেই, মানুষের ক্রমশ বিকশিত বৈজ্ঞানিক উপলব্ধির প্রতীকী হিসেবেও ব্যবহার করা হচ্ছে।
(৩) পশ্চিমবঙ্গের বহু মুসলিম বাঙালী রমণীই প্রতিবেশী হিন্দু মহিলাদের প্রভাবে দুর্গাপূজার সময় অনায়াসে পূজার নতুন শাড়ি কেনেন। গ্রামের মহররমের মেলায় হিন্দু শিশুরা হুটোপাটি করে আসে।
(৪) যেমন, মুসলিম লীগের ১৯৩৬-র সভাপতি ও শুরুর দিকের উদারপন্থী পর্যায়ের একজন প্রথম সারির নেতা, এস, ওয়াজির হাসান। তিনি ১৯৩৮-এর ফেব্রুয়ারীতে একটি চিঠিতে নেহেরুকে লিখেছিলেন, ‘কেবল মুসলমান-হিন্দুদের মধ্যেই নয়, মুসলমানদের নিজেদের মধ্যেও বিকৃতি, মিথ্যা এবং ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ প্রচার শুরু হয়েছিল গত অক্টোবরে মুসলিম লীগের লক্ষ্মৌ অধিবেশনের সভাপতির ভাষণ থেকে। দিনে দিনে সংখ্যালঘুদের অধিকারের মুখোশের আড়ালে সত্যের অপলাপ ও ধর্মীয় বিদ্বেষ আরো বেড়েই চলেছে।’
(৫) যেমন, যখন অন্য ধর্মের নাম না করেও, শুধু হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে বলা হয় যে, এটি পরমতসহিষ্ণু, সবচেয়ে উদার, এর মধ্যে নানা মত ও পথ মিলিত হয়ে এর এক বিশেষ বৃহত্তর রূপ দিয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি, তখন স্বাভাবিকভাবেই এইসব কথার এই অর্থ দাঁড়ায় যে অন্যান্য ধর্ম এরকম পরমতসহিষ্ণু নয়,উদার নয়, নানামতের মিলনক্ষেত্ৰনয় ইত্যাদি। একইভাবে মুসলিমদের অনেকেইএমন কথা বলেন যে, ইসলামেই একমাত্রসাম্য ইত্যাদির কথা আছে, তখন তারও এমন সাম্প্রদায়িক অর্থ দাঁড়ায়।
(৬) আমেরিকায় ঈশ্বরবিশ্বাস ও ধর্মপরিচয় থেকে মুক্ত (atheist ও, nonreligious) ব্যক্তির সংখ্যা মোট জনসংখ্যার মাত্র ৬.৮ শতাংশ (১৯৮০ সালে)। অন্যদিকে মঙ্গোলিয়ায় তা ৬৫ শতাংশ (১৯৯০), উরুগুয়েতে ৩৫.১ শতাংশ (১৯৮০), জামাইকায় ১৭.৭ শতাংশ (১৯৮২), বুলগেরিয়ায় ৬৪.৫ শতাংশ (১৯৮২), ইটালিতে ১৬.২ (১৯৮০) ইত্যাদি। অন্যদিকে যেসব দেশে সমাজতন্ত্রের স্বপক্ষে ব্যাপক গণ আন্দোলন ঘটেছে, অন্তত যেসব দেশ সমাজতান্ত্রিক (বা কমিউনিস্ট) হিসেবে পরিচিত সে সব দেশে এ হার অনেক বেশি, যেমন চীনে ৭১.২ (১৯৮০), কিউবায় ৫৭.১ (১৯৮০), উত্তর কোরিয়ায় ৬৭.৯ (১৯৮০), আলবেনিয়ায় ৭৪.১ (১৯৮০) ইত্যাদি।
(৭) বিবেক দংশন নেই মার্কিনীদের।–হিরোসিমা-নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপের পঞ্চাশ বছর পরেও এই দুষ্কর্ম সঠিক হয়েছে বলে মনে করেন অধিকাংশ মার্কিন নাগরিক। সি বি এস নিউজ ও নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকার এক যৌথ সমীক্ষায় মার্কিনীদের এই অভিমতের কথা জানা গেছে। সমীক্ষার ফল প্ৰকাশ করা হয় সোমবার।
‘২৬ শতাংশ মার্কিন নাগরিক মনে করেন, ১৯৪৫ সালের ৬ই ও ৯ই আগস্ট হিরোসিমা-নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষেপের জন্য আমেরিকার ক্ষমা চাওয়া উচিত নয়। আর ৬৫ বছরের বেশি বয়স্কদের মধ্যে ৮৪ শতাংশই ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না’ বলে জানিয়েছেন।
‘সব মিলিয়ে ৫৮ শতাংশ মার্কিন নাগরিকের বিশ্বাস, এই দুই শহরকে ধ্বংস করা এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা নৈতিকতার মানদণ্ডে বেঠিক কাজ হয় নি। যাদের বয়স ৬৫-এর উপরে তাদের মধ্যে ৬৮ শতাংশই এই মতের শরিক।
‘উল্লেখ্য, দশ বছর আগে অনুরূপ এক সমীক্ষার ফলাফলও ছিল একই। এবারের সমীক্ষাটি ২৩শ্রে থেকে ২৬শে জুলাই পর্যন্ত চালানো হয়েছিল।’ (গণশক্তি; ২৮,৯৫)। তবু আশার কথা আমেরিকাবাসীর বেশকিছু অংশই এইসব মতের শরিক নন। অর্থাৎ তাদের বিবেক দংশন আছে।
(৮) যেমন কয়েক দুশক আগেও ভাবা যেত না যে পৃথিবীর এক পঞ্চমুংশেরও বেশি মানুষ নিজেদের ঈশ্বরবিশ্বাসমুক্ত বা নাস্তিক (atheist) ও ধর্মপরিচয়মুক্ত (nonreligious) হিসেবে প্রকাশ্যে সাগর্বে ঘোষণা করবেন, সরকারিভাবে এই হিসাব নথিভুক্ত হবে এবং তাঁরা সম্মানের সঙ্গে ঘুরেও বেড়াবেন।
(৯) এবং একইভাবে হিন্দুদেরও। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক জানোয়ারেরা এরই সুযোগ নিতে চেষ্টা করে। কিন্তু মানুষের শুভবুদ্ধি ধর্মকেন্দ্ৰিক এই পশুত্বকে প্রতিহত করতে সক্ষম। যেমন, ‘সিউড়ি, ৩ আগস্ট-বীরভূমের খয়রাশোল থানার লোকপুর গ্রামে একটি দুর্গামন্দিরের নাটমন্দিরে মঙ্গলবার রাত্রে দুষ্কৃতীর দল একটি গরুর কটা-মুণ্ডু রেখে যায়। কিন্তু বুধবার এলাকার হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষ মিলিতভাবে ওই ঘটনার প্রতিবাদে এক সম্প্রীতি-মিছিল বের করে ওই চক্রান্ত ভেস্তে দেয়। এদিন এলাকার দোকানপাটও বন্ধ রেখে চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে ‘ধিক্কার দিবস’ পালিত হয়।’ (আজিকাল; ৪-৮-৯৫) ধর্মনিষ্ঠা ও ধর্মান্ধতার মধ্যে, ধর্মের অসাম্প্রদায়িক ও সাম্প্রদায়িক প্রয়োগের মধ্যে এবং অমৌলবাদী ও মৌলবাদী রূপান্তরের মধ্যে মানুষের ধর্মবিশ্বাস দোদুল্যমান থাকে। কিন্তু সচেতন থাকলে ধর্মবিশ্বাসীরাও ধর্মান্ধতা, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদকে যে প্রতিহত করতে পারেন, তা এই ধরনের আরো অসংখ্য ঘটনা থেকে স্পষ্ট।
৫. মৌলবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ
ধর্ম তার বিপন্ন অস্তিত্বের সময় নিজেকে টিকিয়ে রাখতে মৌলবাদের আশ্রয় নেয়। পুঁজিবাদ তার মুমূর্ষ অবস্থায় বেঁচে থাকার মরিয়া চেষ্টায় সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়। উভয়ের সৃষ্টির পেছনেই বিশেষ একটি শ্রেণীর বা তার একাংশের ভূমিকা প্রধান।
ধর্ম ও পুঁজিবাদ দুটিই এক সময় মানব সভ্যতার ইতিহাসের বিশেষ সময়ে জনস্বার্থবাহী, প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু মানুষের সমাজ ও জ্ঞানের বিকশিত পর্যায়ে তাদের প্রয়োজন ক্রমশ ফুরিয়ে আসে বা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের প্রাসঙ্গিকতা আর থাকে না। প্রয়োজন হয়ে পড়ে নতুনতর মতাদর্শের, যা ধর্ম ও পুঁজিবাদের ভিত্তিকে নাড়িয়ে দিয়ে তাদের সরিয়ে দিতে চায়। কিন্তু ধর্ম ও পুঁজিবাদকে সম্বল করে যে কায়েমী স্বাৰ্থ তৈরী হয়ে যায়। তারা নিজেদের অস্তিত্বকে সুরক্ষিত করতে এগুলিকে টিকিয়ে রাখতে বদ্ধ পরিকর থাকে। এদের ঘিরে বিশ্বাস, নির্ভরতা ও অভ্যাসও বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে তৈরী হয়ে যায়। এরাও নতুনতর চিন্তা ও নতুনতর ব্যবস্থাকে স্বাগত জানাতে দ্বিধাগ্রস্ত থাকে। এই দ্বিধার ও বদ্ধপরিকর ইচ্ছার চরম সাংগঠনিক বহিপ্রকাশ ঘটে ধর্ম ও পুঁজিবাদের বিকৃত ব্যবহার তথা মৌলবাদী সংগঠন ও সাম্রাজ্যবাদী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। এবং উভয়েই উভয়ের সাহায্য নিতে পারে বা না-ও নিতে পারে। কিন্তু উভয়েই মানুষের সভ্যতাকে পিছিয়ে নিয়ে যেতে চায়,-ধর্মীয় মৌলবাদ মূলত তার মননকে, সাম্রাজ্যবাদ মূলত তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে, যদিও উভয় ক্ষেত্রেই উভয়ের প্রভাব থাকেই।
ধর্মীয় মৌলবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ। বর্তমানে মানুষের সামনে সবচেয়ে বড় দুটি বিপদ। প্রথমটি মানুষের মনকে আদিম প্রচীন মূল ধর্মীয় বাতাবরণে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে তার বিকাশ ও উত্তরণকে ব্যাহত করে সমস্ত প্ৰগতিশীল বৈজ্ঞানিক চিন্তাকে সক্রিয়ভাবে প্রতিহত করে এবং আরো বিপজ্জনক হল তা মানুষে মানুষে কৃত্রিমভাবে তীব্র বিভেদ সৃষ্টি করে। এই বিভেদ প্রতিহত না হলে তা হিংস্র৷ পারস্পরিক হানাহানিতে মানুষের ও তার সভ্যতার অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলতে সক্ষম। ধর্মপরিচয়ের মত সম্পূর্ণ কৃত্রিম ও আরোপিত একটি পরিচয়কে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে নিজেরই মত আরেকটি মানুষকে ঘূণা করতে, শক্রতে পরিণত করতে, এমনকি হত্যা করতে উৎসাহিত করে ধর্মীয় মৌলবাদ। পাশাপাশি সে আপন ধর্মের শত্রুদেরও সুহৃদের মুখোশ পরায়। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ তার নেতৃত্ব দিলেও সরল ধর্মবিশ্বাসী বহু মানুষকে সে এই বিশ্বাসের কারণে তার চারপাশে জড়ো করে ফেলার ক্ষমতা রাখে।
অথচ এক সময় এই ধর্ম মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হতে শিখিয়েছে, সমাজে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছে। (Religion কথাটিই এসেছে re-digare থেকে যার অর্থ পুনঃসংযুক্ত করা।) তখনকার সমাজ ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তার প্রাসঙ্গিকতা ও উপযোগিতাও ছিল। কিন্তু সমাজে যতই শ্রেণীদ্বন্দ্ব বেড়েছে, ততই ধর্মের বিকৃত ব্যবহার তীব্রতর হয়েছে। শাসকগোষ্ঠী তাকে নিজের শাসন, শোষন ও অস্তিত্বের স্বার্থে মানুষকে ভুলিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছে। এই শ্রেণীবিভক্ত ব্যবস্থার অনুসঙ্গ হিসেবে সৃষ্টি হওয়া ও টিকে থাকা নানা প্ৰতিষ্ঠানিক ধর্মকে তারা নিজেরাও অনুসরণ করেছে, কখনো নিছক নিজস্ব বিশ্বাসের কারণে, কখনো বা সচেতন ভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে। এ কারণেই অ্যারিস্টটল (জন্মঃ খৃ:পূ: ৩৮৪) তাঁর ‘Politics’-এ মন্তব্য করেছিলেন, ‘স্বেচ্ছাচারী শাসককে (অটোক্র্যাট) ধর্মের প্রতি অতিশয় আনুগত্য দেখাতেই হবে। কারণ জনগণ যদি তাকে ধাৰ্মিক বলে মনে করে তবে তার বেআইনি অত্যাচার, নিপীড়নকেও সহ্য করবে এবং তার বিরুদ্ধে সহজে বিদ্রোহও করবে না, কারণ তারা মনে করবে। তার পক্ষেই দেবতারা রয়েছে।’
তাঁর জন্মের প্রায় ১৮০০ বছর পরেও ছবিটা যে পাল্টায়নি, তা বোঝা যায় ম্যাকিয়াভেলি (জন্মঃ ১৪৬৯ খৃস্টাব্দী)-র মন্তব্যে (The Prince)-’রাজপুত্রের পক্ষে সমস্ত ভাল মানবিক গুণাবলী থাকা প্রয়োজন, অন্তত তাকে দেখে সে রকম গুণসম্পন্ন মনে হওয়া চাই, এবং সর্বোপরি, তাকে দেখে যেন পুণ্যবান, ধাৰ্মিক মনে হয়। তাতে যদি কেউ কেউ তাকে অন্যরকম দেখতে পায় তাহলেও তারা কিছু বলবে না.। জনগণের অধিকাংশই মনে করবে। যে সে একজন সম্মানিত ব্যক্তি, যদিও কোনো বিশ্বাসই সে করে না বা ধর্মের প্রতিও তার কোনো আস্থা নেই। তবুও সে শুধু সাধু ব্যক্তির ভান করেই চালিয়ে যাবে, কারণ তার জন্য তো কোনো মূল্যই দিতে হয় না। তদুপরি ধর্মানুষ্ঠান ও ধর্মযাজকদের প্রতি তার বিশেষ আগ্ৰহ দেখাতে হবে।’ (এইভাবে ধর্মের ভান করে মানুষকে প্রতারিত করা ও শাসন করার কৌশলের নির্দেশ সব ধর্মগ্রন্থেই আছে, হিন্দুদের মহাভারত, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্ৰ, মনুসংহিতা ইত্যাদিতে বটেই। বর্তমানের হিন্দু মৌলবাদীদের কাছে এইসব গ্ৰন্থ খুবই মূল্যবান’)
ধর্ম ও শাসকশ্রেণী এইভাবে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত হয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে গোলাম আজম-এর মত মুসলিম মৌলবাদী বা ডঃ মুরলীমনোহর যোশীর মত হিন্দু মৌলবাদীরা আদৌ ইসলাম বা হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী। কিনা বা কতটা বিশ্বাসী এ ব্যাপারে সন্দেহ আছে। আসলে তারা এমন ভান করে যাতে তাদের ‘দেখে যেন পুণ্যবান, ধাৰ্মিক মনে হয়।’ নিক্সন থেকে রাজীব গান্ধী, বিল ক্লিন্টন থেকে নরসিমহা রাও—সবার ক্ষেত্রেই কথাটা হয়তো কমবেশি সত্যি। শাসন ও ধর্মের এই সম্পর্কের কারণেই হয়তো যুধিষ্ঠিরের মত খালি ‘ধর্ম ধৰ্ম’ করা অজঙ্গী শাসকের চেয়ে কৃষ্ণ বা রামের মত যাঁরা ধর্ম আর শাসনের মধ্যে ব্যালেন্স করেছিলেন, তাঁরাই হিন্দু মৌলবাদীদের কাছে বেশি প্রিয় ও কাছের লোক (যদি সত্যিই এরা কোন দিন থেকে থাকেন)।(১) ইসলামী মৌলবাদীদের কাছে একা হযরত মহম্মদই এ ব্যাপারে, একশ’ জনের কাজ করে দিয়েছেন।
বর্তমান পৃথিবীতে সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে অর্থনৈতিক শাসনের (এবং পরোক্ষ রাজনৈতিক শাসনেরও) সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান। সে অনায়াসে একটি দেশের অননুগত সরকারকে ফেলে দিতে পারে, পুরো অর্থনীতিকে কাজ করতে পারে, লক্ষ লক্ষ যুবক যুবতীর সাংস্কৃতিক চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধকে বিকৃত করে দিতে পারে, গাধার সামনে গাজর ঝোলানোর পদ্ধতিতে দরিদ্র দেশের হাজার হাজার মেধাবী ছাত্রছাত্রীকে ক্রীতদাসে পরিণত করতে পারে। এমনকি বাজার দখলের স্বার্থে বোমা মেরে কয়েক লক্ষ মানুষকে মুহূর্তের মধ্যে মেরেও ফেলতে পারে। স্পষ্টতঃই এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অ্যারিষ্টটল-ম্যাকিয়াভেলি-ভীষ্ম-মনু বা মহম্মদের শিক্ষাকে সে-ও তার স্বার্থে ব্যবহার করে। এ করতে গিয়ে সে যে সব সময় ধর্মীয় মৌলবাদী হয়ে ওঠে তা নয়, কিন্তু প্রয়োজনে ধর্মকে ব্যবহার করতে বা ধর্মীয় মৌলবাদীদের সাহায্য করতে সে পিছপা হয় না। তাই দেখা যায় ইরানে যখন ইসলামী মৌলবাদীরা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ভূমিকা নেয় (যদিও সাময়িকভাবে ও নিজের স্বার্থেই), তখন পাকিস্থানের ইসলামী মৌলবাদীরা ঐ সুগ্ন্যুই মত নেয় বা আমেরিকার মৌলবাদীরা শাসকগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে ওঠে।
নব্যপ্রস্তর যুগের শেষ ১০০০ বছরে (অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় ৬ হাজার বছর আগে) ঐতিহাসিকভাবে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সৃষ্টির সময় থেকে ঈশ্বর বিশ্বাস তথা ধর্মের এই শ্রেণী:স্বার্থে ব্যবহার শুরু হয়েছে। কিন্তু ঐ সময়, এবং তারো আগেকার সময়ে, ধর্ম ও ঈশ্বরবিশ্বাস বিভিন্ন মনুষ্যগোষ্ঠীর অবিচ্ছেদ্য একটি অংশ ছিল। জাগরণ থেকে নিদ্রা ও তার মধ্যবর্তী সমস্ত দৈনন্দিন কাজে এই ধর্মীয় চেতনার ঐতিহ্য অনুসারী নির্দেশগুলি সম্পূক্তভাবে মিশে থাকত। গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে বিভেদ থাকলেও এবং একই গোষ্ঠীর মধ্যে দায়িত্বের পার্থক্য থাকলেও, অর্থনৈতিক শ্রেণীর অনুপস্থিতির কারণে এই বিশ্বাসের শ্রেণীগত ব্যবহারও আদিম মানব সমাজে অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু গোষ্ঠীপতির সৃষ্টি, তাকে সাহায্যকারী পুরোহিত শ্রেণীর উদ্ভব এবং কিছু মানুষের হাতে উদ্ধৃত্ত সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলে যে বৈষম্য ধীরে ধীরে, যেন অতি স্বাভাবিকভাবে সৃষ্টি হল, ঐ বৈষম্যকে টিকিয়ে রাখতে ঐসব ব্যক্তিরা ধর্মীয়-ঐশ্বরিক বিশ্বাসকেও কাজে লাগাতে থাকে। নিজেদের প্রতি আনুগত্যকে ঐশ্বরিক নির্দেশ ও ইচ্ছা বলে প্রচার করেছে। যতদিন গেছে, ততই তা তীব্র হয়েছে। কিন্তু তারও পরোকার দীর্ঘ সময় ধরে এই ধর্মবিশ্বাসও কিছু মানুষের সামাজিক আন্দোলনে হাতিয়ারের ভূমিকা পালন করেছে। নতুন দার্শনিক উপলব্ধি, ধর্মের নামে পুরোহিততন্ত্র বা রাজতন্ত্রের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করা, মানবিক ঐক্য ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা, সামাজিক উৎপাদনে ও শিল্প-সাহিত্যে মানুষকে উৎসাহিত করার মত নানা ইতিবাচক কাজ ধর্মকে কেন্দ্র করে বা ধর্মকে ব্যবহার করে মানুষ করেছে। কিন্তু কখনোই ধর্মের শ্রেণী:বহির্ভুত ব্যবহার হয় নি, তা হওয়া সম্ভবও নয়। শাসকশ্রেণী ধর্মকেও তার হাতিয়ার করেছে। আর শোষিত মানুষ তাকে ব্যবহার করেছে একটি অলীক অসহায় আশ্রয়স্থল হিসেবেও,-একটি মানসিক নেশার মত। আফিম যেমন কৃত্রিমভাবে রোগযন্ত্রণা বা ব্যথার অনুভূতি কমায়, কিন্তু মূল রোগটি সারায় না, তেমনি তারাও তাদের দৈনন্দিন জীবনের হতাশা, বঞ্চনা, ব্যর্থতা ও দুরবস্থার যন্ত্রণাকে ভুলে থাকতে ঈশ্বর ও ‘তাঁর’ ধর্মকে আঁকড়ে ধরেছে। কিন্তু এর ফলে এসব সমস্যার সমাধান তো ঘটেইনি, বরং বেড়েছে।
এই শ্রেণীর সৃষ্টি তথা ধর্মের শ্রেণীগত ব্যবহার অর্থনীতির সঙ্গেই যুক্ত। কৃষি পদ্ধতির আবিষ্কার, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সৃষ্টি, শৃঙ্খলার স্বার্থে গোষ্ঠী ও গোষ্ঠীপতির উদ্ভব ইত্যাদি নানা কিছু এর পেছনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। আদিম উৎপাদন ব্যবস্থার উত্তরণ ঘটিয়ে দাস ব্যবস্থা, সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মত সাধারণভাবে বিভক্ত করা অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রতিটি স্তরে ধর্ম ও তার ব্যবহারের রূপান্তর ঘটেছে। রূপান্তর ঘটেছে ধর্মীয় অনুশাসন, মূল্যবোধ ও নীতি বাক্যেরও। আদিমকালে মানুষ যখন শুধুমাত্ৰ ঐশ্বরিক শক্তির কাছে প্রার্থনাদি করেই নিজেদের উৎপাদন ও সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা করেছে, দাসব্যবস্থা ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় এর রূপান্তর ঘটল দ্বিধাহীন আনুগত্যের মানসিকতা সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। এই চরম আনুগত্য ঈশ্বর ও ধর্মের প্রতি যেমন তেমনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি ও ধর্মের রক্ষক হিসেবে প্রচারিত পুরোহিত ও রাজার প্রতিও তথা শাসকগোষ্ঠীর প্রতিও। এই মানসিকতা না থাকলে মুখ বুজে উৎপাদন বাড়ানো যায় না, এক স্বৈরতান্ত্রিক শাসকের অধীনে তথাকথিত সামাজিক শৃঙ্খলাও বজায় রাখা যায় না। ভারতে যেমন দাসপ্রথা প্রচলিত না হয়েও চতুর্বর্ণ বিভাগের মধ্য দিয়ে শূদ্রদের সৃষ্টি করা হয়েছে, যারা সামাজিক ভাবেই দাস-গোষ্ঠী ও একান্ত অনুগত একটি শ্রেণী। প্রকৃতির উপর তথা এক অজ্ঞাত শক্তির উপর নির্ভরতা এই আনুগত্যের শক্তি জুগিয়েছে। (কিন্তু অবশ্যই প্রতিটি স্তরে নানা ভাঙ্গাগড়া ও টানাপোড়েনের সঙ্গে মানুষের নিজস্ব শ্রম, মেধা ও উদ্যমও মিশেছিল, সৃষ্টি হয়েছে নিত্য নতুন দ্বন্দ্ব।)
পাশাপাশি অস্তুত হাজার আড়াই বছর আগে কিছু মানুষের বস্তুবাদী দার্শনিক উপলব্ধিও ঘটেছে। উপলব্ধি করা গেছে ঈশ্বর বিশ্বাস আর এই বিশ্বাসকে কেন্দ্ৰ করে গড়ে ওঠা ধর্ম ও তার অনুশাসনের অসারতা ও ফকির দিকগুলিও। কিন্তু তখন এগুলি মূলত ছিল উপলব্ধিই, যদিও তার সামাজিক ইতিবাচক কিছু দিকও অনুভব করা বা প্রমাণ করা সম্ভব ছিল। (যেমন পুরোহিতদের উচ্ছেদ ঘটিয়ে মানুষের উপর শোষণ ও অত্যাচার কমানো সম্ভব।) তা সত্ত্বেও উৎপাদন ব্যবস্থাকে পাল্টানো এবং ধর্মের ভিত্তিকে নাড়ানোর মত অবস্থা তার ছিল না, কারণ ঐ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই তখনো মানুষের করায়ত্ত হয়নি। এই অজ্ঞানতার পরিবেশে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় তাণ্ডব ও চূড়ান্ত শোষণভিত্তিক সমাজ হাতে হাত ধরে টিকে থেকেছে৷
কিন্তু মূলত ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী থেকে দীর্ঘদিনের বন্ধ্যাত্বি কাটিয়ে মানুষ আবার যুগান্তকারী নানা আবিষ্কার ও জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছে। ব্যপারটি এখন থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে শেষ হওয়া নব্য প্রস্তর যুগের শেষ দু’হাজার বছরে মানুষের একের পর এক যুগান্তকারী নানা আবিষ্কারের সঙ্গে তুলনীয়, —যখন মানুষ মাটির জিনিষ তৈরী করা, লোহা ছাড়া অন্যান্য কিছু ধাতুর আবিষ্কার ও ব্যবহার, কৃত্রিম সেচ-ব্যবস্থা, নদীকে পোষ মানানো, চাকার আবিষ্কার, পাল তোলা নৌকার ব্যবহার, লাঙলের ব্যবহার, চাষের কাজে গবাদি পশুর ব্যবহার, আদিম পঞ্জিকার উদভাবন, সংখ্যার ব্যবহার, ইট আবিষ্কার করে তা দিয়ে ঘরবাড়ি বানানো, লেখার পদ্ধতি তথা আদিম লিপি-ইত্যাদির মত বৈপ্লবিক নানা আবিষ্কার করেছে। স্পষ্টতঃ এগুলি মানুষের জীবন, মনন, অর্থনীতি ও সমাজ সবকিছুকে প্রভাবিত করেছে। উৎপাদন বেড়েছে ও উদ্ধৃত্তি সম্পত্তির সৃষ্টি হয়েছে। তাকে রক্ষা করার জন্য শাসকের প্রয়োজন হয়েছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজ সৃষ্টি হয়েছে।
কিন্তু একসময় এই শ্রেণীবিভাজন তীব্র হওয়ার কারণে মানুষের চেতনাও দাস ব্যবস্থার মত দাসত্বে অভ্যস্ত হয়েছে। ফলে নব্যপ্রস্তর যুগের পরবর্তী ২০০০ বছরে (অর্থাৎ তথাকথিত সভ্যতা শুরুর তথা ঐতিহাসিক যুগ শুরু হওয়ার প্রথম ২০০০ বছরে) মানুষের চিস্তাচেতনায় এই দাসত্বের অনিবাৰ্য প্রতিক্রিয়ায় তার বিজ্ঞানচর্চাও অবরুদ্ধ হয়েছে। দেখা গেছে এই সময়ে মাত্র চারটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার ঘটেছে, যেমন দশমিক পদ্ধতি (২০০০ খৃস্টপূর্বাব্দ), লোহার আবিষ্কার (১৪০০ খৃস্টপূর্বাব্দ), বর্ণমালার আবিষ্কার (১৩০০ খৃস্টপূর্বাব্দ) এবং পয়ঃপ্ৰণালীর আবিষ্কার (৭০০ খৃ খৃস্টপূর্বাব্দ)।
এবং প্রকৃতপক্ষে তারও পরবর্তী প্রায় ২০০০ বছর ধরে অর্থাৎ সমগ্ৰ মধ্যযুগ অব্দি এই অবৈজ্ঞানিক আচ্ছন্নতা ছিল। সামাজিকভাবে বিজ্ঞানচেতনার শূন্যতা পূরণ করতে এই আচ্ছন্নতন্ত্রর একটি বড় অংশ জুড়ে ছিল ধর্ম। ভারত থেকে ইয়োরোপ পর্যন্ত ছিল একই চিত্র, যদিও সর্বত্রই কমবেশি কিছু বৈজ্ঞানিক কাজ ও গবেষণাও চলেছিল কিছু মানুষের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসার প্রেরণায়। মধ্যযুগে খৃস্টান ইয়োরোপে ধর্মচৰ্চা ও ধর্মসাধনাই ছিল মানুষের জীবনের প্রধান কাজ। ভারতসহ অন্যান্য নানা দেশও তার ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে এছবি আস্তে আস্তে পাল্টাতে থাকে। দীর্ঘদিনের জড়তা ও অন্ধত্বের প্রতিক্রিয়ায় হয়তো এক সময় কর্মচাঞ্চল্য ও আলোকের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ধর্মের তথাকথিত রক্ষকেরা এই আলো-কেমোটেই যে সহজভাবে নেয়নি তা অজানা নয়। গ্যালিলিও গালিলি (১৫৬৪— ১৬৪২) বা জিওরদানো ব্রুনো (১৫৪৮-১৬০০)-এর মত বৈজ্ঞানিক মানসিকতার লোকেদের উপর ধর্মীয় অত্যাচারের কথা সুবিদিত। এমনি ভাবেই ধর্মসংস্থার কর্তৃপক্ষীরা যান্ত্রিক ঘড়ির প্রচলনেরও বিরোধিতা করেছিল, কারণ তা হলে তাদের ঘোষণা করা খৃস্টান ধর্ম-মুহূর্তগুলি(২) ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞান চর্চার প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের এমন প্রতিরোধের ঘটনা ঘটেছে। (এখনো যেমন বলা হয় যে, ‘দু পাতা বিজ্ঞান পড়ে ধর্ম-ভগবান মানছে না’)
কিন্তু মধ্যযুগের শেষদিক থেকে একের পর এক অসংখ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার মানুষের সমাজ, উৎপাদন ব্যবস্থা ও মননকে পাল্টাতে থাকে, কিংবা ধর্মান্ধতার প্রতিক্রিয়ায় মানুষের মধ্যে ক্রমশ বেড়ে ওঠা যুক্তিবোধ ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার ফলেই এমন সব আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। ১৪০০-১৬০০ সময়কাল-এটি এই আধুনিক বিজ্ঞানের আবির্ভাবের সময় তথা ইয়োরোপীয় রেনেশার (বা পুনর্জন্মের) কাল, যখন রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও ধর্মব্যবস্থা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য চর্চা, শিল্পকলা ও ভাস্কর্য ইত্যাদি নানা মানবিক ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন ঘটে। (এবং তারই ধারাবাহিকতায় মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চা তথা সত্যের প্রতি অনুসন্ধিৎসা এই বিংশ শতাব্দীতে বিশেষ তীব্ৰতা লাভ করেছে।)
এই রেনেশাঁর ফলে মধ্যযুগীয় পোপতন্ত্রের অবসানে জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হতে থাকে। সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা ও সম্পর্ক ক্রমশ ভেঙ্গে পড়তে থাকে, জন্ম হয় পুঁজিবাদী বা ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি। জন্ম হয় গোঁড়ামিমুক্ত বুর্জেয়া শ্রেণীরও এবং এটিও সুবিদিত, যে এই শ্রেণী প্ৰথমের দিকে ধর্মের বিরুদ্ধেই সোচ্চার ছিল। ধর্মীয় ক্ষেত্রেও রিফর্মেশান আন্দোলন শুরু হয়,-প্রোটেস্টান্টবাদ-উইজম-এর মত খৃস্ট ধর্মের বুর্জেয়া রূপের আবির্ভাব ঘটে। ধর্মকে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার বিরোধিতা করে তথা ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার বন্ধ করে, তাকে শুধু ব্যক্তিগত বিশ্বাসের গণতান্ত্রিক অধিকারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার মানসিকতা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। এই রোনেশী-র ফলেই গণতন্ত্র ও মানবতার পুনর্জন্ম ঘটে।
চিন্তার স্বাধীনতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও রূপান্তর ঘটতে থাকে। দাসব্যবস্থার পরিপূর্ণদাসত্ব ও সমস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রায় দাসত্বের অবস্থান থেকে নতুন উদ্ভূত শ্রমিক শ্রেণীকে নতুন পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মুক্ত করে দেয়, যদিও তার হাতে উৎপাদন ব্যবস্থার উপাদানগুলির মালিকানা দেয় না, উৎপাদিত পণ্যাদির মালিকানাও নয়। এই নতুন ব্যবস্থা শ্রমিকের শ্রম স্বল্পমূল্যে ক্রয় করে নিয়ে মুনাফা বাড়ানোর জন্য তথা সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের জন্য সচেষ্ট থাকে। মুনাফা না বাড়লে পুঁজির বিকাশ ঘটবে না, পুঁজির বিকাশ না ঘটলে পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাটাই ভেঙ্গে পড়বে।
গণতন্ত্র, মানবতা, চিন্তার স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত স্তরে ধর্মের প্রয়োগ, যুক্তিবাদী চিন্তা, বুর্জোয়া নাস্তিকতা ইত্যাদির মত নানা মানবিক মানসিকতার বিকাশের পাশাপাশি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা একদিকে প্রয়োজনীয় ও ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন বিপুলভাবে বাড়িয়ে তোলে,-অন্যদিকে অবাধ প্রতিযোগিতার পরিবেশ, পণ্যনির্ভরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, তীব্র অর্থনৈতিক বৈষম্য ইত্যাদিরও জন্ম দিতে থাকে। এই ধরনের প্রতিযোগিতায় স্বাভাবিকভাবেই মুষ্টিমেয় দু’চারজনই সফল হতে পারে। বিপুল সংখ্যক মানুষের সাফল্য পুঁজির অতিবিভাজন ঘটায় তথা পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই বিরোধী। যত দিন যায়, ততই এই ব্যবস্থা নিজের সৃষ্টি করা সমস্যার জলে আটকে যেতে থাকে। তার থেকে মুক্ত হতে সে নতুনতর কৌশলের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। পুঁজি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে একসময় অবধারিতভাবে মুনাফার হার কমে যায়। এটি পুঁজিবাদের অস্তিত্বের ক্ষেত্রেই সংকটের সৃষ্টি করে। এই সংকট আরো বাড়িয়ে দেয় পুঁজিপ্রয়োগের অসামঞ্জস্যতা। পুঁজিবাদের মূল কথা হল ব্যক্তিগত মালিকানায় ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য উৎপাদন। ফলত যে যার সুবিধা ও পরিকাঠামো মত পণ্যের উৎপাদন করে। আর এর থেকে সৃষ্টি হয় বিশৃঙ্খলা। তৃতীয়ত, অতি উৎপাদনের সংকট পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তোলে। তারা মুনাফা (অর্থাৎ পরোক্ষ শোষণ) করতে করতে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতাই কমিয়ে দিতে থাকে। ফলে পণ্য আর আশানুরূপ বিক্রি হয় না, তাকে নষ্ট করে দিতে হয়। কিন্তু জনগণের মধ্যে বিনামূল্যে তা বিতরণ করে না, করলে পরবর্তী মুনাফার পথ বন্ধ হয়ে যেতে পারে, পণ্যের দামও পড়ে যায়। এই অতি উৎপাদনের আরেকটি পরিণাম একের পর এক কারখানা বন্ধ করে দেওয়া। এর ফলে শ্রমিকরা চরম সংকটের মধ্যে পড়ে, বেকারত্ব বাড়ে, জনগণের ক্রয়ক্ষমতা আরো কমে। সব মিলিয়ে একদিকে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে মানুষের বিক্ষোভ ও জঙ্গী আন্দোলন যেমন শুরু হয়, তেমনি পুঁজিবাদী ব্যবস্থাটিই ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। এক সময় যে ব্যবস্থা মানুষের মনন ও অর্থনীতিকে বিকশিত করার প্রগতিশীল ভূমিকা নিয়েছিল, পরবর্তীকালে তা নিজের অস্তিত্বের স্বার্থে চুড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল গণবিরোধী ভূমিকা নিতে বাধ্য হয়। এরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে তার সাম্রাজ্যবাদী হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে এবং ধর্মকেও নতুন করে ব্যবহার করার তথা ধর্মে আশ্রয় নেওয়ার মাধ্যমে।
সংকট থেকে বাঁচতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহু গবেষণার মধ্য দিয়ে নতুন পথ হাতড়ে বেড়ায়। অন্যের পুঁজিকে যথেচ্ছ বাড়তে দেয় না, নিজের পুঁজির বিভাজন ঘটায় না, বড়জোর নিজ পরিবারের মধ্যে তাকে ভাগ করে। পুঁজিপতিরা পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ করে ও বাজার-গবেষণা করে কারখানা খোলে। জনগণের মধ্যে নিত্যনতুন অনাবশ্যক পণ্যের প্রতি কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি করে (হরলিক্স-কমপ্লান না হলে বাচ্চার শরীর ভাল হবে না, লিপস্টিক-নেলপালিশ না ব্যবহার করলে সুন্দরী হওয়া যাবে না বা ব্যক্তিত্বের বিকাশ হবে না ইত্যাদি অজস্রভাবে)। এর জন্য তাকে হাজারো গবেষণা ও মিথ্যাচার, অর্ধসত্য কথা বলা, চতুর বিজ্ঞাপন, ব্যক্তিত্ব ও মানবতার নতুনতর সংজ্ঞা দেওয়া ইত্যাদির মত অজস্র কাজ করতে হয়।
পুঁজিবাদের প্রথম অবস্থা হচ্ছে অবাধ প্রতিযোগিতার কাল। কিন্তু এর ধারাবাহিকতায় এক সময় অবধারিতভাবে, দ্বিতীয় অবস্থায়, পুঁজির কেন্দ্রীভবন ঘটে তথা কিছু একচেটিয়া পুঁজির জন্ম হয়। ব্যক্তি মালিকানাধীন বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য সৃষ্টি হওয়া এই একচেটিয়া পুঁজি ক্রমশঃ নিজের অস্তিত্বের স্বার্থে বিশ্বের বাজার নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। দরিদ্র, পিছিয়ে থাকা দেশের স্বাধীন শিল্প বিকাশ ও অর্থনৈতিক প্রগতিকে প্রতিহত করে নিজেদের সুবিধাজনক শিল্প, পণ্য ও প্রক্রিয়া চাপিয়ে দিতে থাকে। তা করতে গিয়ে যুদ্ধ বাধাতে আর নিরপরাধ মানুষদের হত্যা করতেও তারা পিছপা হয় না।
এরই প্রতিফলন ঘটেছে, ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারীতে তৈরী পি পি এস-২৩ নামে আমেরিকার চরম গোপনীয় ঐ দলিলে, যেটিতে পররাষ্ট্র দপ্তরের জর্জ কেনান জানিয়েছিলেন, ‘পৃথিবীর ঐশ্বর্যের শতকরা ৫০ ভাগের মালিক আমরা, কিন্তু আমরা পৃথিবীর জনসংখ্যার মাত্র ৬.৩ ভাগ। এই অবস্থায় আমরা ঈর্ষা ও বিদ্বেষের লক্ষ্য না হয়ে পারি না। আমাদের সামনে মূল কাজ হল এমন একটা সম্পর্কের ছক খুঁজে বের করা, যার সাহায্যে আমাদের এই অসাম্যের অবস্থা জিইয়ে রাখা সম্ভব হবে। আমরা, বিশ্বের হিতসাধন কিংবা পরার্থপরতার ব্যয়ভার বহন করতে পারি এরকম চিন্তাধারা দিয়ে নিজেদের প্রতারণার কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। মানবিক অধিকার, জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং গণতান্ত্রিকরণ–এই সমস্ত অস্পষ্ট এবং অবাস্তব লক্ষ্য সম্পর্কে কথা বলা আমাদের বন্ধ করা উচিত। সেদিন আর বেশি দূরে নয় যখন আমাদের প্রত্যক্ষ শক্তি প্রয়োগের ধারণার ভিত্তিতে কাজ করতে হবে। তখন আদর্শবাদী বুলিতে আমরা যত কম বাধাপ্রাপ্ত হই ততই ভাল।’
প্রাকৃতিক ও স্বকীয় কিছু কারণ আমেরিকার এই সম্পদের পেছনে হয়তো, ভূমিকা পালন করেছে, দরিদ্র দেশের মানুষের অযোগ্যতাও হয়তো তাদের দুরবস্থার পেছনে কিছু ভূমিকা পালন করে,-কিন্তু যখন এক ‘ধনী’ ‘দরিদ্রের’ উপর এই ‘প্রত্যক্ষ শক্তি প্রয়োগের’ নীতি গ্ৰহণ করে, তখন আর তা মানবিক থাকে না। অবশ্য এই মানবিকতা ও গণতন্ত্রের কথাবার্তা যে আসলে ভানমাত্র তা-ও স্বীকার করা হয়। যেমন প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে এবং লাতিন আমেরিকায় কেন্যান-বৰ্ণিত আমেরিকান নীতির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ‘আমাদের কঁচামাল রক্ষা করা।’ কাদের হাত থেকে? এইসব দেশের জনসাধারণের হাত থেকে, যারাই আসলে ঐ কঁচামালের মালিক এবং গায়ের জোরে সাম্রাজ্যবাদ তাকে তাদের নিজেদের ‘কাচামাল’ হিসেবে গণ্য করে। আর এই রক্ষা করার কাজ কিভাবে হবে তার উত্তরও স্পষ্ট,–
‘চুড়ান্ত উত্তরটা অগ্ৰীতিকর হতে পারে, কিন্তু স্থানীয় সরকার দিয়ে পুলিশী নিপীড়নে আমাদের দ্বিধা করলে চলবে না।’ এই দ্বিধাহীন নিপীড়ন এখন দেশে দেশে। ঐ সময় (১৯৪৯-এর গোয়েন্দা রিপোর্টে) এও বলা হয়েছিল, কমিউনিষ্টদের কোনোভাবে বাধা না দিতে পারলে আমাদের এই কঁচামাল’ বিপন্ন হতে পারে। এও মনে রাখা দরকার, চল্লিশের দশকের ঐ সময়ে আমেরিকায় ফান্ডামেন্টালিস্টরাও চূড়ান্ত কমিউনিস্ট-বিরোধিতায় নেতৃত্ব দিচ্ছিল, এবং এই সময়ের পর কমিউনিজমএর প্রসার রেখা ও বিভিন্ন দেশে কঁচামাল রক্ষণ করা (একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে)–র মহান’ উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন চরম আকার ধারণ করে। —১৯৫০৫।৩-তে কোরিয়ায় মার্কিন আগ্রাসন, ১৯৫৪-তে গুয়াতেমালায় মার্কিন সামরিক অভিযান, ১৯৫৬-তে মিশরে ব্রিটেন-ফ্রান্স-ইজরায়েলের, ১৯৫০-তে জর্ডান ও লেবাননে মার্কিন ও ব্রিটেনের, ১৯৬০-৬২-তে কঙ্গোয়, ১৯৬১-তে কিউবায়, ১৯৬২তে সেনেগালে প্রেসিডেন্ট সেংঘর-কে ক্ষমতাচ্যুত করার প্রচেষ্টা, ১৯৬৪-৭৫-এ ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসন, ১৯৬৫-তে ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রে মার্কিন হস্তক্ষেপ, ১৯৬৯-৭৫-এ কম্বোডিয়া-লাওসে মার্কিন আগ্রাসন, ১৯৭৩-এ চিলিতে মার্কিন সমর্থনে গণতান্ত্রিক সরকারের পতন, ১৯৭৫-৭৬ ও ১৯৮১-তে অ্যাঙ্গোলায় আগ্রাসন, ১৯৮১-তে মোজাম্বিকে, ১৯৮৩-তে গ্রেনাডায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। তালিকা এখনো শেষ হয় নি।
এইভাবেই ১৯৬৫-তে ইন্দোনেশিয়ার একটি অভ্যুত্থানে আমেরিকা মদত দিয়েছিল। তাতে মারা যায় সাত লক্ষ মানুষ, যাঁদের অধিকাংশই ভূমিহীন কৃষক। কয়েক মাসের মধ্যেই দেশটি আমেরিকার ‘বিনিয়োগকারীদের স্বৰ্গে’ পরিণত হল। নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর একটি প্রবন্ধে একে বলা হল ‘এশিয়ার আলো’। আমেরিকার বহু ‘বুদ্ধিজীবী’-ই এ কাজকে খুব বাহবা দিলেন। তাঁরা বললেন, ‘এই চমৎকার ঘটনাগুলি ভিয়েতনামে আমাদের নীতির প্রাজ্ঞতা প্রমাণ করে।’ নতুনতর কৌশলে, নতুন নতুন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চুক্তির মধ্য দিয়ে এমন আগ্রাসন এখনো অপ্রতিহত গতিতে চলছেই।
বৃহৎ বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি এসবের নেতৃত্ব দেয়। আসলে তারা নিজেদের সংগঠন যে রাষ্ট্র তার মাধ্যমেই এই কাজ করে। তারা নিজেদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা চালায়। সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে বিশাল ক্ষমতাধর এই একচেটিয়া পুঁজি, যা নিজ দেশের বাজার শেষ করে ফেলে বাঁচার জন্য বাইরে থাবা বাড়ায়, যেন প্রাচীন রাজাবাদশার সাম্রাজ্য বাড়ানোর মত। তা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার বিপদগ্ৰস্ত ক্ষয়িষ্ণু বা মুমূর্ষ রূপ, বিপদে পড়ে ক্ষুদ্র পুঁজির উপর আর নির্ভরশীল হয়ে সে বাঁচতে পারছে। না। একদা প্রগতিশীল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার এই রূপান্তর ঘটে বিশেষ শ্রেণীর হাত দিয়েই। এরা সংখ্যায় কম। কিন্তু তাদের ছত্ৰছায়ায় লালিত ও সুবিধাভোগী ব্যক্তির সংখ্যা বিপুল।
অর্থনৈতিক নয়াউপনিবেশবাদ আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। নিজের দেশের বাজার ফুরিয়ে যাওয়ার পর পুজিবাদ এইভাবে, এই রূপে বহির্বিশ্বের জনগণের মধ্য থেকে মুনাফা তথা পুঁজি সংগ্রহের জন্য সচেষ্ট হয়। এ করতে গিয়ে তাকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভাবেও আধিপত্য বা প্রভাব বিস্তুত করতে হয়। এর স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার করতে বা ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদকে মদত দিতেও সে পিছপা হয় না। আমেরিকায় ফান্ডামেন্টালিস্টদের সঙ্গে প্রেসিডেন্টদের গভীর সখ্য কিংবা পোল্যান্ডে খৃস্টীয় মৌলবাদীদের সঙ্গে ‘গণতন্ত্রের’ প্রতিষ্ঠা এরই ফলশ্রুতি। এ ব্যাপারটিও পুঁজিবাদের করুণ সাংস্কৃতিক বা মননগত অসহায়তার পরিচয়। শুরুতে পুঁজিবাদের উদগত বুর্জোয়ারা ছিল উদার ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতার অধিকারী। কিন্তু পরে তাদেরই নিজেদের বিপুল পণ্যবাহী জাহাজকে বাঁচাতে ধর্মের ঝালাই-ও লাগাতে হচ্ছে—যতদিন তা কাজ করে ততদিনই তাদের পক্ষে ব্যাপারটি মঙ্গলকর।
বাঁচার চেষ্টায় তাকে নয়াউপনিবেশে নিজেদের অনুগত এক গোষ্ঠীকেও তৈরী করতে হয়। নানা পুরস্কার, নানা ধরনের বৃত্তি ও অনুগ্রহ প্ৰদান, ভ্রমণ ও ভক্ষণ, সাংস্কৃতিক প্রভাব, আদিম প্রবৃত্তিকে সুড়সুড়ি দেওয়া আনন্দ ইত্যাদির মাধ্যমে তো বটেই,-শ্রেণীচেতনাহীন ও গণ বিচ্ছিন্ন বুর্জোয়া নাস্তিকতা, যান্ত্রিক যুক্তিবাদ, তথাকথিত গণতন্ত্র ও সমানাধিকার (যা প্রায়শঃ বাস্তবত নিজ শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যকার গণতন্ত্র ও সমানাধিকারে পর্যবসিত হয়), আপাত সেবাপরায়ণতা ও সেবামূলক কাজকর্ম, নানা সংস্কারবাদী ক্রিয়াকাণ্ড ইত্যাদি। আপাত মানবিক ও আপাত প্রগতিশীল (অন্তত সামন্ততান্ত্রিক বাতাবরণের পরিপ্রেক্ষিতে) নানা ভাবেও নিজেদের বন্ধুমনোভাবাপন্ন ও নিজেদের প্রতি সহানুভূতিশীল গোষ্ঠীর সৃষ্টি করে। এমনকি নিজেদের ক্ষমতার অস্তিত্ব বজায় রাখতে ও পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতির নাম করে, বিপদগ্ৰস্ত অবস্থায় তথাকথিত বামপন্থীরাও সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি একচেটিয়া পুজিকে স্বদেশে আমন্ত্রণ করে আনে।
ধৰ্মীয় মৌলবাদের মত সাম্রাজ্যবাদও এইভাবে যাদের শাসন ও শোষণ করা হবে তাদেরই মধ্যে নিজের অনুগৃহীত অনুগত বাহিনী তৈরী করে। কারণ এটি স্পষ্ট যে, শোষিত মানুষের একাংশই যদি তাদের সাহায্য করে তবে এই শাসন, শোষণ ও আধিপত্য নিশ্চিত দীর্ঘস্থায়িত্ব অর্জন করবে। কিন্তু ধর্মীয় মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা সাধারণ সরল ধর্মবিশ্বাসী মানুষদের অসহায় ধর্মবিশ্বাসকে কাজে লাগায়—উৎসাহিত করে পিছিয়ে থাকা অবৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনাকে। আর সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া পুঁজি কাজে লাগায় পিছিয়ে থাকা দেশের স্বচ্ছন্দ্যকামী মানুষদের উন্নততর চিস্তার আকাঙ্খা, শ্রম ও মেধাকে,—উৎসাহিত করে আত্মকেন্দ্রিকতা, যান্ত্রিকতা ও পরনির্ভরতাকে।
পুঁজিবাদের মুমূর্ষ অবস্থা যেমন সাম্রাজ্যবাদ, তেমনি ধর্মের বিপদগ্ৰস্ত, ক্ষয়িষ্ণু বা মুমূর্ষ অবস্থা ধর্মান্ধতাত, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় মৌলবাদ। বিবর্তনবাদ থেকে বস্তুবাদী দর্শনের মত নানা বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ এবং পরিবর্তিত উৎপাদন ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কের কারণে ঈশ্বরকেন্দ্ৰিক ধর্মের তথা ভাববাদী দর্শনের ভিত্তি কেঁপে ওঠে। তার আদিম ও প্রাচীনকালের প্রয়োজনীয়তাও কমে আসে (যখন ম্যাজিক ও ধর্মানুশাসন উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করত)। দলে দলে মানুষ ঈশ্বরবিশ্বাস ও ধর্মপরিচয় থেকে মুক্ত বলে নিজেদের ঘোষণা করতে থাকে। (বর্তমানে যেমন প্রায় ১১৫ কোটি পৃথিবীবাসী এই দলভুক্ত)। এ অবস্থায় ধর্ম নিজেকে বাঁচাতে মরিয়া হয়ে ওঠে। ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিদের ও ধর্মজীবী শ্রেণীর নিজস্ব সংকটের অসমাধান ব্যাপারটিতে ইন্ধন জোগায়। হিংস্র অন্ধভাবে ধর্মানুসরণের মধ্যে এই সংকটের সমাধান খোঁজার চেষ্টা করে। তারা নিজ ধর্মীয় সম্প্রদায়কে এক কাট্টা করে ভিন্ন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে মুক্তির পথ খোজে। তারা ধর্মের মূল অনুশাসন ও নিয়মনীতিকে ফিরিয়ে এনে আনন্দময় ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে। ধর্মীয় মৌলবাদ শুধু ধর্মের এই মূলে ফিরে যাওয়ার আকাঙ্খা নয়, তা ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতার রসে জারিতও বটে। সাম্রাজ্যবাদ। এই ধর্মকেন্দ্রিক উন্মত্ততা ও বিপথগমনকে উৎসাহিত করে, কারণ সে অনুভব করে এর ফলে তার গায়ে অন্তত আচড়টি পড়বে না। পরিস্থিতি বিশেষে তাই ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ সাম্রাজ্যবাদের বড় প্রিয় বন্ধু, বড় আপন জন।
কিন্তু ধর্মের এই নাজেহাল অবস্থার পেছনে বুর্জেয়াদের তথা পুঁজিবাদের উদ্ভবই বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। শুরুর দিকে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা পুঁজিবাদ ও ঐ উপযোগী৷ উদার বুর্জেয়া মানসিকতাকে রুখতে সর্বশক্তি দিয়ে ধর্মকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে, কারণ তার অস্তিত্বের সঙ্গে ধর্ম ও ভাববাদ গভীরভাবে সংযুক্ত (এবং এখনকার ধর্মান্ধতা-সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদের মধ্যে তারই ধারাবাহিকতা বর্তমান)। পাশাপাশি পুঁজিবাদও তখন চেষ্টা করেছে ধর্মের ভাববাদী কুয়াশা সহ সামন্ততন্ত্রকে হটাতে। কারণ তার বিকাশের জন্য এই অবৈজ্ঞানিক ভাববাদী পরিমণ্ডল ছিল বাধাস্বরূপ। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার চেয়ে কম অনিশ্চয়তায় ভরা, কম প্রকৃতি নির্ভর এবং অনেক বেশি মনুষ্য-ও বিজ্ঞান-নির্ভর। তখন অলৌকিক শক্তির বা ধর্মীয় অনুশাসনের ভাবালুতার চেয়ে বাস্তববাদী, যুক্তিনির্ভর, বস্তুকেন্দ্ৰিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও মানসিকতার প্রয়োজন ছিল বেশি। তাই প্রয়োজন হয়েছিল নতুনতর আইনকানুন, রাষ্ট্ৰীয় ব্যবস্থা, মূল্যবোধ ও রীতিনীতির। বেদ-বাইবেলের চেয়ে ফিজিক্স-কেমিস্ট্রিই তখন প্রধান পাঠ্য হয়ে ওঠে। দরিদ্রকে অন্নদান করে পুণ্য অর্জনের চেয়ে, তাদের চাকরি দিয়ে ও শ্রমকে কাজে লাগিয়ে উৎপাদন বাড়ানো বেশি গুরুত্ব পেতে থাকে।
রেনেশাঁর ধারাবাহিকতায় যে আধুনিক জ্ঞান ও মানসিকতার বিকাশ ঘটে, তাতে প্ৰতিষ্ঠানিক ধর্মের চিরাচরিত অবস্থান ও ঐতিহ্যনির্ভর মূল্যবোধ-রীতিনীতির প্রতি এই আলোকিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রশ্ন ও সন্দেহ জাগে। সৃষ্টি হয় বুর্জেয়া নাস্তিকতা, অধাৰ্মিকতা ও যুক্তিবাদ। এসবের প্রতিক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠানিক ধর্মকে বাঁচাতে খৃস্টীয় রিভাইভ্যালিজম বা ধর্মীয় পুনরভুত্থানবাদ ও ফান্ডামেন্টালিজম বা মৌলবাদের ও সৃষ্টি হয়েছে, সৃষ্টি হয়েছে ধমীর্য নানা রিফর্মেশান আন্দোলন,-পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ধর্মকে গ্রহণযোগ্য রূপে টিকিয়ে রাখার জন্য। কিন্তু পরবর্তীকালে বুর্জেয়ারা যখন নিজেরাই সংকটে পড়ে তথা পুঁজিবাদের ক্রম ঘনায়মান বিপদ অনুভূত হয়, তখন তাদের একাংশের মধ্যে আবার ধর্মকে ব্যবহার করার বা ধর্মে আশ্রয় নেওয়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। সামন্ত প্ৰভুদের মত পুঁজিপতিরাও ক্রমশ অনুভব করল শ্রমিকদের মধ্যে ধর্ম ও ঈশ্বর বিশ্বাস গভীরভাবে টিকে থাকলে তাদের ক্ষোভ ও হতাশা অনেক কমে যায়, তাদের থেকে আনুগত্যও বেশি পাওয়া যায়। তাই জৈন ব্যবসায়ীরা বা বিড়লারা বিশাল মন্দির বানায় বা জিন্ডাল অ্যালুমিনিয়াম কোম্পানির ফ্যাকটরির মধ্যে মন্দির গড়ে ওঠে। আমেরিকাইংল্যাণ্ডে চার্চের পুনরায় রমরমা শুরু হয়। ব্যাপারটি প্রধানতঃ, ক্রমশ পরিস্ফুট হতে থাকা পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার অনিশ্চয়তা ও সংকটের প্রতিফলনও বটে। একজন পুঁজিপতির সর্বস্বাস্ত হওয়া, মুনাফা কমে যাওয়া, প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়া—এই ব্যবস্থায় এ সবের কোনটিই যে চূড়ান্তভাবে আটকানো সম্ভব নয় তা পরের দিকে ক্রমশ পরিষ্কার হয় (যেন প্রকৃতিনির্ভর কৃষি উৎপাদনের মত)। এই ব্যবস্থার এই যে অদেখা, অজানা, সামাজিক প্রতিকূল শক্তি, সেটিরও প্রতিফলন ঘটতে থাকে বুর্জেয়া, পুঁজিপতি এমনকি জনসাধারণের মধ্যেও—একদা যেমন ঘটেছিল অজ্ঞাত রহস্যময় প্রাকৃতিক প্রতিকূল শক্তির প্রতিফলনে অলৌকিক শক্তিকল্পনার সৃষ্টির সময়ে। এর ফলে বুর্জেয়া পুঁজিপতিরাও ধর্মে তার প্রাথমিক অনীহা ত্যাগ করে ধর্মশ্রিয়ী হতে থাকে। পাশাপাশি প্রকৃতিকে জয় করার ক্ষেত্রে এখনো মানুষের বিপুল অসম্পূর্ণতাও প্রতিফলিত হয় এই ধর্মাশ্রয়ের প্রক্রিয়াতে।
কিন্তু শুরুর দিকের ইতিবাচক বুর্জেয়া মূল্যবোধগুলিও টিকে থাকে,–সেই মানবতা, গণতন্ত্র, তথাকথিত সমানাধিকার (আসলে তা বুর্জোয়াদের নিজেদের মধ্যেকার সমানাধিকার), ধর্ম ও ঈশ্বরকে অস্বীকার করার প্রবণতা তথা নাস্তিকতা, ধর্মকে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের স্তরে নিবদ্ধ রাখা ইত্যাদি। তবে পরিবর্তিত পরিবেশ পরিস্থিতেতে তাদের বিকৃতি ঘটে। এই বিকৃতি মূলত ঘটে। পুঁজিবাদের দ্বিতীয় স্তরে, তার সাম্রাজ্যবাদী রূপান্তরের কালে। টিকে থাকার মরীয়া চেষ্টায় সে সাংস্কৃতিক ও চেতনাগত বিকৃতি, হিংস্রতা ও বিকৃত যৌনতার মত নেতিবাচক প্রবৃত্তিকে উৎসাহিত করা, অপ্রয়োজনীয় পণ্যের বন্যা, নিত্যনতুন কৌশাল, চুক্তি, আগ্রাসন, ষড়যন্ত্র, রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বঁধানো বা ধর্মীয় মৌলবাদকে মদত দেওয়ার মত নানা অমানবিক অগণতান্ত্রিক ক্রিয়াকাণ্ডে লিপ্ত হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সামাজিক প্রয়োগের চেয়ে ক্রমাগত ব্যক্তিগত স্বার্থে তার প্রয়োগের অবশ্যম্ভাবী। পরিণামও তাই হতে বাধ্য।
বর্তমান সময়ে ধর্মও তার প্রাথমিক সারল্য, অসচেতন বিশ্বাস, ভালবাসা, উদারতা, মানবিকতা ইত্যাদি হারিয়ে ক্রমশঃ ক্রুর, অসহিষ্ণু, জনবিরোধী, অনৈক্য সৃষ্টিকারী ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থে ধর্মকে ক্ৰমাগত ব্যবহারের পরিণামও হয়তো তাই। এরই চূড়ান্ত একটি রূপ মৌলবাদ, যা ভিন্ন ধর্মের মানুষকে শত্রু বলে গণ্য করতে শেখায়, যা মানুষের মনকে’ প্ৰাচীন ও এখন অপ্রাসঙ্গিক পরিবেশে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, রুদ্ধ করতে চায় আলোর দিকের অভিসারকে। আসলে ধর্মের এই বিবর্তন ঘটে বিশেষ শ্রেণীর হাতে, যারা নিজেদের বাঁচাতে শ্রেণীবিভাজনের চেয়ে ধর্মীয় বিভাজনকে ও বৈজ্ঞানিক দর্শনের পরিবর্তে ভাববাদী দর্শনকে তীব্রভাবে উপস্থাপিত করে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমস্ত সুফল আত্মসাৎ করেও মৌলবাদীরা বৈজ্ঞানিক দর্শনকে অস্বীকার করে। এমন কি তাকে ব্যবহার করে ধর্মীয় মৌলবাদ প্রচারের জন্যও। (হাই-টেক মৌলবাদী প্রচার ও ধর্মপ্রচার!!) ধর্মীয় মৌলবাদ যেমন যান্ত্রিকভাবে বিজ্ঞানের প্রয়োগ ঘটায়, সাম্রাজ্যবাদও তেমনি বিজ্ঞানচেতনার চেয়ে বিজ্ঞানের মুনাফাদায়ী প্ৰযুক্তিকেই প্রধান গুরুত্ব দেয়।
এ কারণে উভয়ের সাধারণ শত্রু হচ্ছে বস্তুবাদী দর্শন, সমাজতন্ত্র ও কম্যুনিজম। ধর্মীয় মৌলবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ উভয়েই সর্বশক্তি দিয়ে, ছলেবলে কৌশলে তাকে প্রতিরোধ করতে চায়। উভয়ের শত্রু যখন এক, তখন তাদের নিজেদের মধ্যকার মিত্ৰতাও অস্বাভাবিক নয়। কমিউনিজমকে আটকাতে তাই পোল্যান্ডে খৃষ্টীয় ধর্মীয় মৌলবাদ মাথাচাড়া দেয়। এগুলি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরই আরব্ধ কাজ। তাকে পরিপূর্ণতা দেওয়ার দায়িত্ব নেয়। ধর্মীয় মৌলবাদ। কিন্তু কখনো আবার পরিস্থিতি অনুযায়ী তারা পরস্পরের সাময়িক বিরোধী ভূমিকাও পালন করে, যেমন ঘটেছে। ইরানে কিংবা সম্প্রতি ভারতের মহারাষ্ট্রে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে হলেও শিবসেনা-বিজেপির দ্বারা আমেরিকার এনরনের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করার মধ্য দিয়ে।
কমিউনিজম-এর তত্ত্ব যথার্থ কি যথার্থ নয়, কিংবা তার সম্পূর্ণতা ও বাস্তবতা কতখানি, এসব প্রশ্ন অবাস্তর। কিন্তু এটি সত্য যে, সাম্রাজ্যবাদ ও ধর্মীয় মৌলবাদ উভয়েরই কমিউনিজম বিরোধিতার প্রশ্নে কোন দোদুল্যমানতা নেই। সাময়িক ও সংকীর্ণ স্বার্থে কখনো মৌলবাদী শক্তিরা (যেমন মুসলিম লীগ বা বিজেপি) বামপন্থীদের সঙ্গে একদা আপোষ ও বাহ্যিক ঐক্য গড়লেও, তা কখনোই কমিউনিজমের সঙ্গে ঐক্য নয়, বরং তা কমিউনিজমের নামাবলী গায়ে চাপানো সুবিধাবাদীদের সঙ্গে অতি ভঙ্গুর এক জোট মাত্র। সাম্রাজ্যবাদের পক্ষেও এই সংকটাপন্ন সুবিধাবাদী বামপন্থীদের সঙ্গে আপোষ অসম্ভব নয়। তবে প্রায়শ প্রাথমিক উদ্যোগটা আসে। দ্বিতীয়দের কাছ থেকেই। আর উদারপন্থী বুর্জোয়ারা বামপন্থীদের সঙ্গে বিষয়ভিত্তিক ঐক্য গড়তেই পারেন এবং ধর্মীয় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা রুখতে ধর্মনিরপেক্ষ বুর্জেয়াগোষ্ঠীর সঙ্গে বামপন্থীদের এমন ঐক্য একটি সুস্থ ব্যাপারই।
ধর্মীয় মৌলবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ উভয়েই ভিত্তিমূলে কমিউনিজম বিরোধিতা করতে বাধ্য হয়, কারণ মতাদর্শগতভাবে এটি তাদের উভয়েরই অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক। (আমেরিকার ফান্ডামেন্টালিস্টদের কাছে বিবর্তনবাদ বা ইয়োরোপের খৃস্টীয় ‘মৌলবাদীদের কাছে গালিলেও প্রমুখের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণও একইভাবে বিপজ্জনক বলে প্রতীয়মান হয়েছে।) এই বিরোধিতার ক্ষেত্রে তারা সর্বাধিক আন্তরিক এবং কোন আপোষ করতে রাজী নয়। কিন্তু তাদের উভয়ের মধ্যে প্রয়োজনে আপোষ বা পরোক্ষ প্রশ্রয়ের ব্যাপার ঘটতে পারে। এর একটি পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রশ্নে হিন্দু ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও মৌলবাদীদের মধ্যে। এই মৌলবাদীরা ভিন্ন ধর্মের মানুষের বিরুদ্ধে (যারা তারই দীর্ঘদিনের প্রতিবেশী ও বন্ধু ছিল) যতটা না সোচ্চার ছিল, তার অতি সামান্য অংশে সোচ্চার ছিল সাম্রাজ্যবাদী ও ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে। গান্ধীবাদী বা সন্ত্রাসবাদী যে পথেই হোক না কেন হিন্দু-মুসলিম-শিখ নির্বিশেষে বহু ধর্মবিশ্বাসী মানুষই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সাংগঠনিকভাবে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী দল বা গোষ্ঠীগুলি সাধারণভাবে এর থেকে দূরে থেকেছে—তাদের প্রধান শত্রু ছিল সাম্রাজ্যবাদ নয়, ভিন্ন ধর্মের মানুষ।
সাভারকর একসময় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছেন। কিন্তু ১৯২০-এর দশকে ও তার পর তিনি হিন্দুত্বের প্রধান তাত্ত্বিক প্রবক্তা ও হিন্দুমহাসভার নেতার ভূমিকাই মূলত পালন করেন। ১৯৪২-এর আন্দোলনের সময় বিভিন্ন পৌর ও স্থানীয় প্রতিষ্ঠান, আইনসভা এবং বিভিন্ন চাকুরিতে মহাসভার সদস্যদের তিনি নিজ নিজ পদে অবিচলিত থেকে দৈনন্দিন কর্ম করে যেতে’ নির্দেশ দিয়েছিলেন। যুদ্ধের সময় তাঁর শ্লোগান ছিল ‘রাজনীতির হিন্দুকরণ ও হিন্দুধর্মের সামরিকীকরণ’। এর অর্থ দাঁড়ায় তীব্র মুসলিম বিরোধিতা ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতা। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে সাভারকার গোপনে ভাইসরয়কে বলেন যে, হিন্দুদের ও বৃটিশদের বন্ধু হওয়া উচিত এবং প্রস্তাব করেন যে কংগ্রেস মন্ত্রীসভাগুলি পদত্যাগ করলে হিন্দুমহাসভার কংগ্রেসের বিকল্প হিসেবে থাকা উচিত। (জোটল্যান্ডের প্রতি লিনলিথগো, ৭ অক্টোবর, ১৯৩৯)।
১৯২৯ সালে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আর. এস. এস)-এর প্রধান কর্মধ্যক্ষ বা সংঘচালক হিসেবে মনোনীত হওয়া হেডগেওয়ার নিজে সত্যাগ্ৰহ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং কারাবরণ করেছিলেন। কিন্তু ১৯৩০-৩১-এর আইন অমান্য আন্দোলনসহ অন্যান্য নানা আন্দোলনে আর এস এস-এর ভূমিকা নগন্য। ১৯৪০এর নাগপুরে অফিসারদের’ প্রশিক্ষণ শিবিরে যোগ দিয়ে হেডগোওয়ার বলেছিলেন, ‘আমি আমার সামনে হিন্দুরাষ্ট্রের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ দেখতে পাচ্ছি।’ স্বাধীনতার চেয়ে এই হিন্দুরাষ্ট্রই ছিল তার প্রধান লক্ষ্য। তাই তার পরবর্তী সরসংঘচালক গোলওয়ালকর সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ উভয়কেই এক করে ‘বিদেশী’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন এবং উই আর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইনড’ বইতে এই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নীরবই থেকেছেন। উল্টে তিনি বৃটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদের সমালোচনা করে মন্তব্য করেছেন, ‘আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ এবং সর্বজনীন বিপদের তত্ত্ব থেকে আমাদের জাতিত্বের ধারণা তৈরী হয়েছে। এর ফলে আমাদের প্রকৃত হিন্দু জাতিত্বের ইতিবাচক অনুপ্রেরণা থেকে আমরা বঞ্চিত হয়েছি। এবং আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বহু আন্দোলনই নিছক বৃটিশবিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়েছে। বৃটিশ বিরোধিতার সঙ্গে দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদকে সমার্থক করে দেখা হয়েছে। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, তার নেতৃবর্গ এবং সাধারণ মানুষের উপর এই প্রক্রিয়াশীল মতের প্রভাব সর্বনাশা হয়েছে।’
স্পষ্টতঃই এই হিন্দু মৌলবাদীদের কাছে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার চেয়ে হিন্দুজাতিত্ব বা হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তা সাম্রাজ্যবাদের হাত ধরে ও তার শোষণকে টিকিয়ে রেখে হলেও তাদের কিছু যায় আসে না।(৩) এবং এটিও আসলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শিক্ষারই ফল। অন্যান্য দেশের ইতিহাস বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ, আধুনিক যুগ হিসেবে চিহ্নিত হলেও, বৃটিশরাই ভারতীয় ইতিহাসকে হিন্দুযুগ, মুসলিম যুগ, ও বৃটিশ যুগ (‘খৃষ্টান যুগ’ নয়) হিসেবে চিহ্নিত করেছে। মুসলিম লীগ-এর জন্মের অনেক আগেই বৃটিশ শাসক স্যার হেনরি এলিয়ট ভারতের হিন্দু ও মুসলিমদের দুটি পৃথক জাতিসত্তা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। মিল (Mill)-এর মত বৃটিশ ঐতিহাসিকেরা অবৈজ্ঞানিক ভাবে ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে ভারতীয় ইতিহাসকে পূর্বোক্ত তিনভাগে বিভক্ত করে ‘হিন্দুযুগ’ ও ‘মুসলিম যুগ’-কে সাম্প্রদায়িক রঙে রাঙিয়ে দিয়েছেন। সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ও ঐ মানসিকতায় পরিশীলিত এইসব ঐতিহাসিকেরা হিন্দুদের সাধুসন্ন্যাসী ও মুসলিমদের অত্যাচারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অর্থনৈতিক শ্রেণীগত বিভেদ ও দ্বন্দ্বকে অস্বীকার করে স্যার হেনরি এলিয়টের মত বৃটিশ শাসকরা এমনও মন্তব্য করেছেন যে, ‘… মুসলিমদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে হিন্দুদের হত্যা করা হয়েছে, হিন্দুদের ধর্মীয় মিছিল ও পূজা ইত্যাদিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, মূর্তি ভাঙ্গা হয়েছে, মন্দির ধ্বংস করা হয়েছে, জোর করে ধর্মান্তরকরণ ও বিয়ে করা হয়েছে’ ইত্যাদি ইত্যাদি।
সাম্রাজ্যবাদ তার স্বার্থে সর্বদা চেষ্টা করে। এইভাবে একপেশে, বিকৃত, আংশিক ইতিহাসকে তুলে ধরার মধ্য দিয়ে শাসিতদের বিভাজিত করতে এবং সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ঐক্যকে বিনষ্ট করতে। ভারতের হিন্দু ও মুসলিম মৌলবাদীরা এই সাম্রাজ্যবাদী প্রচারকেই লুফে নিয়েছে। কারণ তারাও শাসিত ও শোষিত জনগণকে ধর্মের মত একটি কৃত্রিম পরিচয়ে বিভাজিত করতে চায়। মানসিকতার এই ঐক্য কখনোই সাম্রাজ্যবাদ ও মৌলবাদকে পরস্পরের চরম বিরোধী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। আর তাই দেখা যায় বৃটিশ বিরোধী সত্যাগ্ৰহ আন্দোলন, ভারত ছাড় আন্দোলন, আজাদ হিন্দ ফৌজ ও তার বিচার, বোম্বাই-এর নৌবিদ্রোহকে কন্দ্র করে ১৯৪৫-৪৬-এর উত্থান ইত্যাদি কোনটিতেই কি আর এস এস কি মুসলিম লীগ কেউই নিজেদের জড়ায় নি, এবং এই সময় তারা নিজেদের সংগঠিত করার চেষ্টা করেছে। পরোক্ষ বৃটিশ সহযোগিতার দ্বারা। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর বৃটিশরা যে অত্যাচারের বন্যা বইয়েছে, এইসব ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক তথা মৌলবাদী ‘দলগুলির উপর তার প্রায় কোন ছিটেই লাগে নি। উপরন্তু এদের সাম্প্রদায়িক আন্দোলনে বৃটিশবিরোধী সংগ্রামই দুর্বল ও বিভ্রান্ত হয়েছে। পাকিস্তানের জন্য জঙ্গী আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় হিন্দুরা আর এস এস-কে রক্ষাকর্তা হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে, এমন কি কংগ্রেসের একটি অংশের মধ্যেও এই মানসিকতা সৃষ্টি হয়েছে। বাংলার মত মুসলিম অধূষিত এলাকায় বাম ও প্রগতিশীল শক্তিগুলি আর এস এস-এর উত্থান রোধ করতে পারলেও সারা দেশের পরিপ্রেক্ষিতে এসময় এটি তার শক্তিবৃদ্ধিই ঘটিয়েছে। যুদ্ধের ঠিকাদারি ও বাড়তি মুনাফার ফলে সৃষ্টি হওয়া বণিক গোষ্ঠীর বড় অংশ তাদের অর্থের জোগানও দিয়ে গিয়েছেন।
সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতার সঙ্গে ধর্মীয় মৌলবাদের বন্ধুত্বের স্বাভাবিক প্রবণতাই রয়েছে এবং তার ভিত্তি হিসেবে কাজ করে গণবিরোধী শ্রেণীস্বার্থ। (কিন্তু এই স্বার্থে ঘা লাগলে তারা পরস্পরের বিরোধিতা করতেও পিছপা হয় না।) তাই আমেরিকা ফান্ডামেন্টালিস্টরা রাষ্ট্রকে আরো সশস্ত্র করার দাবী জানায়, হিরোসিমা-নাগাসাকির উপর বোমাবর্ষণ বা ভিয়েতনাম যুদ্ধের বর্বরতায় অনুতপ্ত না হওয়া এই ধরনের মানসিকতারই একটি প্রকাশ। তাই বিলি গ্রাহামের মত ফান্ডামেন্টালিস্ট নেতৃত্ব টুমান-আইসেনহাওয়ার থেকে জনসন-নিক্সনের পরম সুহৃদ হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সেই দেশেই শ্ৰীবৃদ্ধি ঘটে অন্যান্য মৌলবাদীদের নানা সংগঠনেরও। যেমন ক্যালিফোর্নিয়ায় রয়েছে ‘ফেডারেশান অব হিন্দু অ্যাসোসিয়েশনস’। (এরা ১৯৯৫-এর ‘বর্ষসেরা হিন্দু বা ‘Hindu of the Year’ উপাধিতে সম্মানিত করেছে। পিতাম্বারা ও বাল থ্যাকারে-কে। পরের বছরের জন্য মনোনীতদের তালিকায় অন্যতম। নাম-উমা ভারতী ও টি এন শেষন।) আর মহেশযোগী থেকে প্রভুপাদ-অসংখ্য বদমায়েস ধর্মজীবীদের রমরমা বাজারের পরিবেশও ঐসব দেশই।
পোল্যান্ডের মত দেশ সাম্রাজ্যবাদ ও ধর্ম তথা মৌলবাদের গাঁটছড়া বাঁধার আরেকটি উদাহরণ। একদা সে দেশ ছিল সমাজতন্ত্রের নামধারী কিন্তু অসমাজতান্ত্রিক। সমাজতন্ত্রের মুখোশপরা পোল্যান্ডে ধর্মের রমরমা শুরু হয়েছিল। ১৯৩৭ সালে সে দেশে পাদ্রীর সংখ্যা ছিল ৯৫৩০, কিন্তু ১৯৭০-এ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল ১৩৭৬৫তে। চার্চের সংখ্যা ৫১২০ থেকে বেড়ো হয় ১১৭০৯। লক্ষ লক্ষ কপি ধর্মীয় বই ও পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এ সবই খৃস্টীয় মৌলবাদের পথ পরিষ্কার করছিল। পাশাপাশি অর্থনৈতিক ভাবেও তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক পোল্যান্ডে পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ ঘটছিল। এসব কারণে ‘শেষ পর্যন্ত সেখানে ‘গণতন্ত্রের’ নামে সোভিয়েত সমর্থিত প্রতিবিপ্লবী সরকারকে হটিয়ে দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অপর এক প্ৰতিবিপ্লবী সরকারী-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও ক্যাথলিক চার্চের নিয়ন্ত্রণাধীন এক সরকার। কিন্তু এই সত্যটি গোপন করার জন্য সারা বিশ্ব জুড়ে সাম্রাজ্যবাদী প্রচার মাধ্যমসমূহ তাদের একনায়কত্বমূলক প্রচারণার মাধ্যমে এই পরিবর্তনকে ‘সমাজতন্ত্রের’ বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের বিরাট বিজয় হিসেবে আখ্যায়িত করেছে এবং শ্রমিক সহ শ্রমজীবী জনগণের এক বিরাট অংশ এই প্রচারণার শিকার হয়ে অনেক ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষ অবলম্বন করছে এবং সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ বলতে কিছু নেই এই ধারণার বশবতী হয়ে নিজেদের শ্রেণী স্বার্থের বিরোধিতায়, সাময়িকভাবে হলেও, নিযুক্ত হচ্ছে।’ (বদরুদ্দীন উমর, অনীক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৯০) ফ্যাসিবাদের সঙ্গেও ধর্মের তথা ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তির এমন গাঁটছড়া বাধা অস্বাভাবিক নয়। ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ধর্মীয় মৌলবাদ-সবাইয়ের জনবিরোধী চরিত্রের মিল তাদের অবস্থা বিশেষে পরস্পরের সুহৃদ করে তোলে। পোল্যান্ডকে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ধর্মের সহযোগী হওয়ার একটি প্রতীকী উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। একইভাবে ইটালি ও জার্মানিতেও ফ্যাসিবাদের সঙ্গে ধর্মের এই সহযোগী ভূমিকার কথা জানা আছে। এখানে ধর্ম (ক্যাথলিক চাৰ্চ) একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার ভূমিকা পালন করে। আসলে এসব ক্ষেত্রেই ধর্ম বৃহত্তর অর্থের নিছক একটি বিশ্বাস নয়, সেটি শাসকশ্রেণীর একটি গণবিরোধী প্ৰতিষ্ঠানিক হাতিয়ার, যে হাতিয়ার মৌলবাদেরই রকমফের মাত্র।
ইটালিতে ফ্যাসিবাদের উত্থানে ও শক্তিশালী হওয়ার পেছনে ভ্যাটিকানের বিরাট ভূমিকা ছিল। ১৯২১-এ ভবিষ্যতের পোপ পিউস-১১ (Pius XI) মুসোলিনি সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘মুসোলিনির মত একজনকে আমাদের খুব দরকার,–ঈশ্বরই (Providence) তাকে আমাদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য পাঠিয়েছেন। উদার চিন্তার আচ্ছন্নতা থেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে মুক্ত।’ ১৯২৩-এর জানুয়ারী মাসে রাষ্ট্রের ধর্মীয় (papal) সেক্রেটারী, কার্ডিন্যাল গ্যাসপেরি এই ফ্যাসিষ্ট নেতার সঙ্গে বৈঠকের ব্যবস্থা করেন, যাতে তাঁর সঙ্গে একটি চুক্তিতে আসা যায়। গ্যাসপেরি মন্তব্য করেছিলেন, ‘এই মুসোলিনি। যদি কোনদিন পূর্ণ ক্ষমতায় আসে, তবে আমরা যা চাই সেটিই আমরা পেয়ে যাব।’ পোপ হওয়ার পরও পিউস-১১ মুসোলিনিকে সমর্থন করার জন্য ক্যাথলিক কেন্দ্রীয় দল (Catholic Centre Party)-র নেতাদের নির্দেশ দিয়ে বলেন, ‘তিনি ঈশ্বর প্রেরিত ব্যক্তি।’
১৯২৯ সালে ভ্যাটিকান ইটালির ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে একটি চুক্তি (concordatঅর্থাৎ পোপ তথা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে রাষ্ট্রের চুক্তি) করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্ৰীয় ধর্ম হিসেবে রোমান ক্যাথলিক ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করা এবং এসবের ফলে সরকার থেকে চার্চ ১ কোটি ৯০ লক্ষ পাউন্ড অনুদানও পায়। প্রোটেস্টান্টদের মধ্যে গড়ে ওঠা আমেরিকান ফান্ডামেন্টালিজম-এর মত রোমান ক্যাথলিক গোষ্ঠীও যে একই ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী তাতে কোন সন্দেহ নেই, যদিও ‘ফান্ডামেন্টালিস্ট’-এর ছাপ তার নেই, কিন্তু মৌলবাদী চরিত্রের প্রায় সবটুকুই রয়েছে। নাৎসি-জার্মানির তিন মুখ্য ফ্যাসিস্ট নেতৃত্ব—হিটলার, গোয়েকেবলস ও হিমলার-সবাই ছিল একনিষ্ঠ রোমান ক্যাথলিক। কঠোর যান্ত্রিক শৃঙ্খলা ও প্রশ্নহীন দ্বিধাহীন আনুগত্য ফ্যাসিবাদ ও ধর্মীয় মৌলবাদের টিকে থাকার প্রধান শর্ত। এ কারণেই রাষ্ট্ৰীয় স্বয়ং সংঘ বা জামাতে ইসলামী তাদের সংগঠনকে ‘ক্যাডার ভিত্তিক’ করে গড়ে তোলে এবং এদের কাজেকর্মে কথায় বার্তায় ফ্যাসিস্টদের ছায়া স্পষ্ট অনুভব করা যায়। এই একই বৈশিষ্ট্য ছিল নাৎসীদেরও। ধর্মীয় কর্তৃত্বের প্রতি আনুগত্য, সত্যের তথা যুক্তির প্রতি সম্পূর্ণ অনীহা, আর অমানবিকতা-পোপের অধীন ক্যাথলিক ধর্মের এই ধরনের শিক্ষা হিটলাররাও পেয়েছে। ইট্ৰলির মত জার্মানিতেও প্রতিষ্ঠানিক ধর্মের এই রূপ ফ্যাসিস্টদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করে। এই কারণেই দেখা যায় জার্মানির পার্লামেন্টে (রাইখস্টাগ-এ) হিটলারকে যে একটি ভোটের গরিষ্ঠতায় একনায়কতান্ত্রিক ক্ষমতা (dictatorial power) দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছিল ঐ ভোটটি (decisive vote) দিয়েছিল ক্যাথলিক সেন্টার পাটি। হিটলার ক্ষমতা পাওয়ার ছ’ মাসের মধ্যেই ১৯৩৩-এর ২০শে জুলাই, পোপ হিটলারের সঙ্গে চুক্তি (concordat) করেন।
হিটলার কোনদিনই সরকারীভাবে চার্চ ত্যাগ করেননি। ক্যাথলিকরা অনেক বইকে নিষিদ্ধ করলেও (যেমন গ্যালিলেও-দের), কখনোই হিটলারের ‘মাইন কাম্পফ’ (Mein Kampf) এই নিষিদ্ধ তালিকায় ওঠেনি। অথচ গ্যালিলিওরা যখন একটি বৈজ্ঞানিক সত্যকে তুলে ধরেছিলেন, তখন মাইন ক্যাম্পফ’ ছিল জাতিভেদ ও হিংস্রতায় ভরা। হিটলার নিজেও স্বীকার করেছেন, তিনি ‘মার্কসীয় সন্ত্রাসবাদ’ ও ও ‘ধর্মীয় অনুশাসন’ থেকে শিক্ষাগ্ৰহণ করেছেন, তবে সবচেয়ে বেশি শিক্ষা পেয়েছেন ও উৎসাহিত হয়েছেন খৃস্টীয় গোষ্ঠীর থেকে (Jesuit Order থেকে)। নিজের উচ্চপদাধিকারী এস এস বাহিনীর সদস্যদের তিনি খুসন্ট সংঘ’ (Society of Jesus) নামে অভিহিত করতেন এবং অন্ধবিশ্বাস ও কঠোর শৃঙ্খলার ব্যাপারে শিক্ষা নিতে তাদের বিশেষ কিছু ধর্মগ্রন্থ (যেমন Spiritual Exercises of Ignatius of Loyola) পড়তে নির্দেশ দিতেন। এই শিক্ষায় শিক্ষিত নাৎসি প্রচার বিভাগীয় প্রধান গোয়েকেবলস একসময় মন্তব্য করেছিলেন, ‘চার্চ যদি কালো-কে সাদা বলে। তবে আমি তাইই বিশ্বাস করব।’ আরেক শীর্ষস্থানীয় নাৎসি নেতা হিমলার তার ডায়েরিতে লিখেছিলেন, ‘যাই-ই ঘটুক না কেন আমি সবসময় ঈশ্বরকে ভালবাসব, তার কাছে প্রার্থনা করব, ক্যাথলিক চার্চের প্রতি বিশ্বস্ত থাকব এবং আমাকে যদি তার থেকে বহিষ্কারও করা হয়, তবু তাকে সমর্থন করে যাব।’ (Heinrich Himmer; Roger Manvel 3 H. Frankeal) (এছাড়া ‘The Psychopathic God, Rober G. L. Waite 44° ‘History of the SS, Graber ইত্যাদি)
ধর্মের মূল শিক্ষা অন্যকিছু বলে যতই বলা হোক না কেন, ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে যে অবৈজ্ঞানিক যুক্তিহীন মানসিকতা ও অন্ধ আনুগত্য সম্পৃক্তভাবে মিশে থাকে তা। এইভাবে ফ্যাসিবাদের সৃষ্টিকে উৎসাহিত করে, ধর্মের মৌলবাদী রূপান্তরে ভূমিকা পালন করে এবং ধর্মের গণবিরোধী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশও ঘটায়। আসলে বিশ্ব মানবতা, প্রেম, অহিংসা, সবার প্রতি সমদৃষ্টি ইত্যাদি জাতীয় ধর্মের এইসব তথাকথিত মূল শিক্ষা’-গুলি ঈশ্বর ও ধর্মের নাম না করেও অনায়াসে বলা যায় এবং সেটিই সুস্থ ও কাম্য ব্যাপার, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি। তা না করে এগুলি ধর্মের নামে প্রচার করতে গিয়ে এই শিক্ষাগুলিকে প্রতিষ্ঠা করা তো যায়-ই নি, উপরন্তু মৌলবাদ ও ফ্যাসিবাদের মত অপশক্তিগুলির সৃষ্টিকেই উৎসাহিত করা হয়েছে।
রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এই যুক্তিহীনতা ও অন্ধ আনুগত্য একনায়কতন্ত্র ও ফ্যাসিবাদকে আমন্ত্রণ করে আনে। যেমন ভারতের বেশ কিছু লোক প্রয়াত রাজীব
উপাধিকারী এরা ব্যক্তিগতভাবে যাই-ই হোন না কেন, দেশের ও দেশের মানুষের স্বার্থে কোন সংগ্রামের ইতিহাস বা কোন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান যে তাদের নেই-তা স্পষ্ট। তবু ঈশ্বরের সামনে হামাগুড়ি দেওয়ার মত বা রাজার সামনে নতজানু হওয়ার মত এমন হাস্যকর উন্মাদের (যেন রাজনৈতিক জোকারের) দল এদেশে যথেষ্টই রয়েছে। অন্যদিকে শৃঙ্খলা রক্ষার নাম করে কিছু কিছু কমিউনিষ্ট নামধারী ‘ক্যাডারভিত্তিক’ রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের মধ্যেও এই ধরনের স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতা ও যুক্তিবুদ্ধিহীন আনুগত্যকে উৎসাহ দেওয়া হয়। একনায়কতন্ত্র, ফ্যাসিবাদ, স্বৈরতন্ত্র ইত্যাদি এদের ঘাড়ে চেপেই আবির্ভূত হয়, এরাই পরিস্থিতি বিশেষে নয়াফ্যাসিবাদ বা ধৰ্মীয় ও রাজনৈতিক মৌলবাদের ক্যাডারেও পরিণত হয়।
ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় ১৯৪৫-এ অর্জিত হয়েছে বলে মনে করা গেলেও, তার সঙ্গী ও সস্তানেরা এখনো রয়েছে-ধর্মীয় মৌলবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে। এই সাম্রাজ্যবাদ ও মৌলবাদ সর্বত্র ও সর্বদা চেষ্টা করে জনসাধারণের উপর অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে। তার জন্য তারা বিশেষ ক্ষেত্রে নিজেদের সুবিধাজনক পরিস্থিতিতে পরস্পরের হাতে হাত মেলাতেও প্রস্তুত। গণবিরোধী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্য উভয়েই অনুভব করে যে অর্থনৈতিক আধিপত্য টিকিয়ে রাখতে গেলে ধর্মমোহ একটি বড় সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম।(৪) এরজন্য তারা জনগণের সমস্ত বিপ্লবী প্রচেষ্টা এবং শোষণমুক্ত, শ্রেণীহীন বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে টুটি টিপে মেরে ফেলতে চায়। তার জন্য অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নানা কৌশল তারা অবলম্বন করে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রসার ঘটিয়ে কিছু মানুষের আপাত স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করা যেমন এর একটি দিক, তেমনি নিজেদের ধর্মীয় ঐতিহ্যকে রক্ষা করে ধর্মীয় গোষ্ঠীগত স্বাতন্ত্র্য, জাতীয়তাবাদ ও ঐক্য প্রতিষ্ঠা করার প্রতিশ্রুতিও অন্য একটি দিক।
কিন্তু এর ফলে আপামর জনসাধারণের স্বাচ্ছন্দ্য আন্দেী অজিত হয় না, মাঝখান থেকে কিছু দেশ ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির মত সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নয়া ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক দাসে পরিণত হয় এবং স্বদেশেরই ও স্বধর্মেরই কিছু শাসক-শোষকের অধীনে ক্ৰমশঃ বেড়ে চলা বৈষম্য, দারিদ্র্য ও সংকটের দিকে এগিয়ে যাওয়া হয়। এমনকি আমেরিকার মত অগ্রসর’ দেশের জনসাধারণের একটি বড় অংশই গৃহহীন, দরিদ্র, বেকার, অসহায় জীবনে ক্রমশ পতিত হয়। রমরমা ঘটে (অন্তত সাময়িকভাবে) শুধু সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধি বৃহৎ বহুজাতিক সংস্থার (একচেটিয়া পুঁজির) ও কিছুটা তার প্রতিনিধি-কর্মচারীদেরও, কিন্তু উভয়ের চূড়ান্ত স্থায়িত্বও এই ব্যবস্থা দিতে অক্ষম। অন্যদিকে ধর্মীয় মৌলবাদীরা বিশেষ ধর্মের মূলভিত্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে যে ঐতিহ্যকে রক্ষা করার কথা বলে, তার ফলে মানুষে মানুষে সম্প্রীতিই বিনষ্ট হয় এবং কৃত্রিম বিভাজন বাড়ে মাত্র। কৃত্রিম ধর্মপরিচয়ের চেয়ে মানুষ হিসেবে নিজের ও অন্যের পরিচয়ই যে একমাত্র ও বড় পরিচয় ঐ বোধ সে ভুলিয়ে দেয়। বিজ্ঞানমনস্কতার পরিবর্তে ভাববাদী দর্শনের অন্ধকারে মানুষের মনকে নিমজ্জিত করে। সাম্রাজ্যবাদ মুনাফার তথা পণ্যবিক্রির স্বার্থে জড়বাদী ও ভোগবাদী মানসিকতায় ভুলিয়ে এবং ধর্মীয় মৌলবাদ জঙ্গী ভাববাদে নেশাগ্ৰস্ত করে মানুষকে ও তার সভ্যতাকে ক্রমশঃই এক বৃহৎ সংকটের দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। উভয়েই মানুষকে তার প্রকৃত অবস্থান, সমস্যা, সমস্যার স্বরূপ ও তার সমাধানের উপায় সম্পর্কে সচেতন হতে অতি সক্রিয়ভাবে বাধা দেয়।
পৃথিবীর নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের মুক্তির পথ খুঁজতে গিয়ে একসময় মানুষ মার্কসীয় দর্শন তথা সাম্যবাদী-সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের সন্ধান পেয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে এই দর্শনই চরম সত্য, সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত এবং শতাধিক বছর। পরেও সে অপরিবর্তনীয়। মার্কসীয় দৰ্শন নিজেই এই মৌলবাদী মানসিকতার বিরোধী। কিন্তু ক্ৰমশঃ পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতিতে এই ধরনের নানাবিধ দার্শনিক মতাদর্শের থেকে শিক্ষা নিয়ে কিভাবে জড়বাদ-ভোগবাদ-বৈষম্যবাদ-শোষণবাদের মোকাবিলা করার উপায় ও তত্ত্ব আবিষ্কার করা যাবে, সেই পথ অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক চেতনাকেই দুর্বল ও বিকৃত করে দেয় সাম্রাজ্যবাদী প্রচার ও মৌলবাদী মানসিকতা। এখনো পর্যন্ত জানা তত্ত্বগুলির মধ্যে মার্কসীয় দর্শন জনগণের বৃহত্তম অংশের স্বাৰ্থবাহী বলে প্রতিষ্ঠিত এবং সাম্রাজ্যবাদ-মৌলবাদ মানুষের একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের স্বাের্থবাহী বলে প্রমাণিত। তা সত্ত্বেও এখনকার পৃথিবীতে মানুষ ও তার সমাজ এই সাম্রাজ্যবাদী-মৌলবাদী মানসিকতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য প্রস্তুত বলেই প্রতীয়মান হয়, যে কারণে এখনো এরা শক্তিশালী এবং একইসঙ্গে, প্রাসঙ্গিকভাবে, শক্তিশালী মানুষের হিংস্রতা, উগ্ৰপন্থা, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও অনৈক্যের মানসিকতা, অসহিষ্ণুতা এবং (পুজিবাদ প্রচারিত) ভোগবাদী বা (ধর্মাচরণের নামে) ভাববাদী মনোবৃত্তি। অন্যদিকে মানুষ এখনো যথাসম্ভব মার্কসীয় দৰ্শন বা এই ধরনের আরো বিকশিত যে মতাদর্শ মানুষকে শ্রেণীহীন, শোষণমুক্ত, মানবিক ঐক্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে, তার জন্য প্রস্তুত নয়। পাশাপাশি বহু মানুষের মধ্যেই অসততা, শ্রমবিমুখতা, সুবিধাবাদী স্বার্থপরতা, ক্ষমতালিন্সা ইত্যাদি এখনো তীব্রভাবে রয়েছে, রয়েছে বহু বিচিত্র ধরনের স্বার্থগত, শ্রেণীগত ও গোষ্ঠীগত দ্বন্দ্ব। এসবের প্রতিফলন ঘটে যারা এই মতাদর্শকে অনুসরণ করার কথা বলে তাদের বহুজনের আপাত বিচ্যুতি, ব্যর্থতা ও বিভ্রান্তির মধ্যে। এবং এই মতাদর্শকে প্রয়োগ করার ব্যবহারিক দিকগুলি সাময়িকভাবে ভেঙ্গে পড়ার মধ্য দিয়েও। ঐতিহাসিক নিয়মে আপনা থেকেই এসব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে-এমন নিয়তিবাদী, স্বতস্ফুৰ্ততানির্ভর মানসিকতা অবশ্যই বিপজ্জনক এবং অবশ্যই সচেতন প্ৰয়াসে ও সক্রিয় উদ্যোগে ছবিটিকে পাল্টানো দরকার। এই পাল্টানোর ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ ও মৌলবাদ উভয়ের মূলোচ্ছেদ ঘটানো অন্যতম প্রাথমিক শর্ত।
এটি হয়তো ঠিক যে চরম অর্থে বৈষম্যহীন সমাজ কোনদিনই মানুষ অর্জন করতে পারে না। এর বড় একটি কারণ মানুষ যন্ত্র বা ছাঁচে গড়া কোন বস্তু নয়। মানুষ তার আবেগ ও আকাঙ্খা নিয়ে পরস্পরের থেকে পৃথক। এই পার্থক্যের পেছনে নার্ভকোষ থেকে শারীরিক নানা দিক তথা জীন-গত (genetic) কারণ যেমন রয়েছে, তেমনি আছে চতুষ্পপাশ্বের জাগতিক প্রতিফলন এবং বিগত বহু সহস্র বছরের বিচিত্র অভিজ্ঞতার পুরুষানুক্ৰমিক ধারাবাহিকতাও। এই ধারাবাহিকতার প্রতিফলন শুধু মানুষে মানুষে ঘটে না, তার ছোট বড় অজস্ৰ গোষ্ঠীর মধ্যেও ঘটেছে। এই বৈচিত্ৰ্য নিয়েই মানুষ ও তার সমাজ। এই বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে ও তার আবেগকে মূল্য না দিয়ে, মানুষকে যন্ত্রের মত একটি আরোপিত মত বা আদর্শকে অনুসরণ করায় বাধ্য করলে, এক সময় সে বিদ্রোহ করবেই। এইভাবেই যে দীর্ঘকালীন মানসিক ও সামাজিক প্রস্তুতি তাকে তার নানাবিধ শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার উপযোগী, স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলবে, সেই ধৈর্যশীল প্রক্রিয়া এড়িয়ে গিয়ে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ধর্ম–এদের উৎখাত করার প্রচেষ্টা একসময় ব্যর্থ হতে বাধ্য।
একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় ও প্রয়োজনে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ধর্মের সৃষ্টি। মানব সভ্যতার একটি বিশেষ পর্যায়ে উভয়ের বিপদ ও অপ্রয়োজনীয়তা ধীরে ধীরে অনুভব করা যাচ্ছে। এটিও অনুভব করা যাচ্ছে যে, এ দুটি বস্তুগত ও মনোগত পদ্ধতিই সাম্রাজ্যবাদের মত ভয়াবহ ও মৌলবাদের মত বিপজ্জনক সামাজিক অপশক্তির জন্ম দিতে পারে এবং দিয়েছেও। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ধর্ম-এদের টিকিয়ে রেখে সাম্রাজ্যবাদ ও মৌলবাদ উভয়ের চূড়ান্ত মূলোচ্ছেদ করা ও পুনরাবির্ভাবকে প্রতিহত করা সম্ভব নয়। মানুষের সভ্যতার যে পর্যায়ে এ দুটির অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদ ও মৌলবাদের আবির্ভাব ঘটে নি, সেই সময় মানুষ পেরিয়ে এসেছে বিগত শতাব্দীতেই। এখন তাদের বিদায়ের পালা। কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মানুষের বিগত নৃত্যুনতম ৬-৭ হাজার বছরের অভ্যাসকে দুই-এক শত বছরে পুরোপুরি উচ্ছেদ করার চিন্তা কতটা বাস্তব সম্মত তা বিচার করা অতি গুরুত্বপূর্ণ। এটিও বিচার করার প্রয়োজন যে, বর্তমান পর্যায়ে এ দুটির সামাজিক উপযোগিতা, প্রয়োজনীয়তা ও মানুষের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা আরো কতটা রয়েছে। তাদের এই উপযোগিতা, প্রয়োজনীয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যদি ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ধর্মের মূলোচ্ছেদ করার জঙ্গী আপোষহীন ও বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা চালানো হয়, তবে এই অকালবোধনের প্রতিক্রিয়ায় মানুষের মধ্যেই ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ধর্ম—উভয়কে আরো অন্ধভাবে আঁকড়ে ধরার প্রবণতা সৃষ্টি হতে বাধ্য এবং তা হচ্ছেও।
কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুধু এই কারণে স্তিমিত করাটা বিপজ্জনক। পরস্পর সম্পর্কিত, পরস্পরের সুহৃদ এবং একই সমাজব্যবস্থার কাঠামো ও উপরিকাঠামো হিসেবে প্রতিষ্ঠিত এই দুই সভ্যতা-বিরোধী অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই স্তিমিত করার অর্থ, দুর্বলতার সুযোগে তাদের শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করা এবং বৈষম্যমুক্ত বৈজ্ঞানিক চেতনাসম্পন্ন নতুন মানবসমাজ প্রতিষ্ঠার কাজকে বিলম্বিত করা। এর জন্য সরাসরি এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও ধর্মের স্বরূপ সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত প্রচার ও তার জনস্বার্থবিরোধী দিকগুলির বিরুদ্ধে সংগ্রামও করা প্রয়োজন। কিন্তু তার লক্ষ্য হওয়া উচিত সেই শ্রেণী যারা মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তির মোহ ও প্রয়োজন এবং ধর্ম ও ঈশ্বর-বিশ্বাসে মোহ ও প্রয়োজনকে ব্যবহার ক’রে তাদের শাসন, শোষণ ও প্রতারণা করে। বিভিন্ন স্তরের শোষিত মানুষকে এ ব্যাপারে। সচেতন করা, সংগঠিত করা ও বৈজ্ঞানিক সত্য জানতে সাহায্য করা যায়, এবং এইভাবেই তাদের স্বাবলম্বী হয়ে মুক্তির পথ খোঁজার উপযুক্ত করে গড়ে তোলার চেষ্টা চালানো যায়। কিন্তু তা করতে গিয়ে এখনো মানুষ তার যে অসহায়তা, অনিশ্চয়তা, অজ্ঞতা ও আবেগের কারণে ব্যক্তিগত সম্পদ ও ধর্মকে আকড়ে রাখতে চায়, সেগুলিকে অস্বীকার করে মানুষকে অপমান, হতমান ও আঘাত করা অপরাধ।
এবং অপরাধ মানুষের শারীরিক, মানসিক তথা আবেগগত বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে তাকে যন্ত্রে পরিণত করা বা যন্ত্রের মত ব্যবহার করার মানসিকতাও। ‘আমি (নেতা) যা বলছি, সেটিই সত্য, আর তার অনুসরণ যে না করে সে ভ্রান্ত ও শত্ৰুস্থানীয়’-এমন মানসিকতা মূলত কর্তৃত্ববাদী, পিতৃতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানিক ধর্মের হলেও এই মানসিকতা এখনকার, রাজনৈতিক দল, এমন কি তথাকথিত বামপন্থীদের মধ্যেও সংক্রমিত।
মানুষের সমাজে বাস করতে গেলে প্রতিটি মানুষকেই নির্দিষ্ট কিছু বিধিনিষেধ, আচারবিধি ও শৃঙ্খলা মানতেই হয়; সমাজে বিশেষ একজনের চূড়ান্ত ব্যক্তিস্বাধীনতা ও চরম গণতন্ত্র অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু তা যান্ত্রিকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে কিনা এবং কাদের স্বার্থে এই শৃঙ্খলা ও আচারবিধি—এগুলি বিচার করা অবশ্যই অতি গুরুত্বপূর্ণ। যান্ত্রিকতা-মুক্ত একটি বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ ও পথ মানুষকে তার সভ্যতার স্থায়িত্বের দিকে নিয়ে যাবে, যে স্থায়িত্বকে রক্ত লোলুপ সাম্রাজ্যবাদ ও চেতনাবিকৃতকারী মৌলবাদ অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। বর্তমান সময়ে মার্কসীয় দর্শনকে অনুসরণ করার কথা বলা কিছু ব্যক্তিদের মধ্যে মানুষকে যন্ত্র হিসাবে ও একই ছাঁচে ফেলা আদর্শ একটি সত্তা হিসেবে ভাবার এবং ব্যবহার করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেলেও, প্রকৃতপক্ষে এই দর্শনই মানুষকে তার সামগ্রিকতার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করার কথা বলে। মানুষের নিজের মধ্যে, পরস্পরের মধ্যে ও সমাজের সঙ্গে নিরস্তুর ঘটে চলা দ্বন্দ্ব ও মিলনের প্রক্রিয়া এই দর্শনের অন্যতম দিক। ‘যান্ত্রিক মার্কসবাদীরা’ বা ‘মার্ক্সিস্ট মৌলবাদীরা’ তাদের আচরণে এসব অস্বীকার করে। অধৈৰ্য, অসহিষ্ণু, সুবিধাবাদী এরাই মার্কসবাদের নামে সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি করে।
প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদ ও মৌলবাদই মানুষকে এক যন্ত্রে পরিণত করে। সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া পুঁজি তার অস্তিত্বের স্বার্থে মানুষকে এক পণ্যক্রেতা, মুনাফাদাতা যন্ত্র হিসেবেই দেখে। মানুষ সম্পর্কে তার প্রধান বিচার্য কোন দেশের মানুষের মধ্যে বাজার ভাল, কারা বেশি মুনাফা দেবে। তার কাছে মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তার স্বাধীন মূল্য ততটা নেই, যতটা আছে। এই স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তাকে কিভাবে পুঁজির স্বার্থে লাগানো যায় তার চিন্তাটি। ধর্মীয় মৌলবাদও যান্ত্রিকভাবে ধর্মানুসরণকে উৎসাহিত করে। একজন ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি যান্ত্রিকভাবে সারা দিন রাত নানা ধর্মীয় আচার ও সংস্কারগত খুঁটিনাটি মেনে চলেন। তার একটু ব্যতিক্রম হলেই খুঁতখুঁতানি শুরু হয়। মৌলবাদ এর ওপর আরো রঙ চড়ায়। সে মানুষকে মানুষ হিসেবে না দেখে, একটি বিশেষ ধর্মপরিচয়ের অধীনস্থ হিসেবে বিচার করে। মানুষের স্বাধীন অস্তিত্ব তার কাছে মূল্যহীন। জন্মসূত্রে একজন হিন্দু বা মুসলিম কিভাবে চলবে, কিভাবে চিন্তা করবে, কি চোখে ভিন্নধর্মাবলম্বী প্রতিবেশীদের দেখবে তা ঠিক করে দেওয়ার ঠিকাদারি নেয় মৌলবাদ (ও সাম্প্রদায়িকতা)। একইভাবে সাম্রাজ্যবাদও ঠিকাদারি নেয়। তার অর্থনৈতিক উপনিবেশের মানুষরা কিভাবে চিন্তাভাবনা করবে, কিভাবে নাচ-গান করবে, তাদের ব্যক্তিত্ব কেমন হবে, তারা কি কেনাকাটা করবে, কি খেলে ভাল থাকবে, কি বানাবে ইত্যাদি সবকিছু ঠিক করে দেওয়ারও।
এগুলিকে পরিহার করে এবং প্রতি মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্ৰ্যকে মর্যাদা দিয়ে চরম অর্থে বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়তো বাস্তবত অসম্ভব। সম্প্রতি জানা আপেক্ষিকতার তত্ত্ব বা কোয়ান্টাম তত্ত্ব জাতীয় কিছু বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও প্রকল্পের সামাজিক প্রয়োগ এ ব্যাপারে নতুনভাবে ভাবতেও হয়তো বাধ্য করবে। তবু আপাতত এই সমাজের জন্য চেষ্টা করাটাই বৈজ্ঞানিক ও সুস্থ ব্যাপার। অন্তত এই প্রচেষ্টা বৈষম্য ও শোষণকে নূনতম করবে, প্রতি মানুষের সুস্থভাবে বেঁচে থাকার প্রতিশ্রুতি পালন করবে। আর তা না করার অর্থ এই বৈষম্য বাড়তে দেওয়া এবং সাম্রাজ্যবাদ-মৌলবাদের হাতকে তথা শাসকশ্রেণীর হাতকে শক্ত হতে দেওয়া। পৃথিবীর কোন দুটি বট গাছের গড়ন, পাতার সংখ্যা ইত্যাদি হুবহু এক নয়। এই বৈচিত্র্য থাকলেও সবগুলিই বটগাছই বটে। একইভাবে দুটি মানুষের মধ্যেকার যে পার্থক্য তা বাহ্যিক, ও ততটা গুরুত্বপূর্ণও নয়, যতটা গুরুত্বপূর্ণ এই সমগ্র মানবজাতির অন্যতম সদস্য হিসেবে তার পরিচয়টি। তাই আপাত কিছু বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা সত্ত্বেও সমগ্র মানবজাতির ঐক্য অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু তা অর্জন অদূরভবিষ্যতেও হবে কিনা সন্দেহ। তবু তার প্রচেষ্টাই বৈজ্ঞানিক, সুস্থ ও কাম্য। তা না করার অর্থ মানুষের মধ্যকার অনৈক্য, অবিশ্বাসকে বাড়তে দেওয়া। এবং তা করার অর্থ সাম্রাজ্যবাদ ও মৌলবাদের মত অপশক্তির বিরুদ্ধে নিরলস লড়াই করাও। সদা সত্য কথা বলিবো’-র মত নির্দেশ চরম অর্থে আজীবন মেনে চলা দুরূহ ও প্রায় অসম্ভব একটি ব্যাপার। তবু তাকেই অনুসরণীয় হিসেবে সামনে রাখাটাই কাম্য, তা না হলে মিথ্যারই বিপুল ব্যাপ্তি ঘটবে। একইভাবে চুড়াস্ত বৈষম্যহীন, শোষণমুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ সমাজের লক্ষ্যই সামনে থাকাটা কাম্য-অন্যথায় অনৈক্য, বৈষম্য ও শোষণকেই বাড়তে দেওয়া হবে মাত্র। সাম্রাজ্যবাদ ও ধর্মীয় মৌলবাদ উভয়েই এই বৈষম্য, শোষণ ও অনৈক্যাকে উৎসাহিত করে। তাই অন্যান্য নানা সামাজিক অপশক্তি তথা গণশত্রুর মত তাদের উচ্ছেদের লক্ষ্যও সমস্ত সচেতন, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের জীবনেরই একটি অংশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত।
অনাবিল ধর্মবিশ্বাস আছে, মৌলবাদ নেই, কিংবা তারও পরোকার, সেই কৈশোরের পুঁজিবাদ আছে সাম্রাজ্যবাদ নেই। —এমন হলে হয়তো কত সুন্দরই হত এই পৃথিবীটা। ২ কিন্তু তা আর হবার নয়। মানুষের সভ্যতার ইতিহাস সময়ের স্রোতে ঐ কাল পেরিয়ে এসেছে। তাকে আবার পশ্চাদগমনে ফেরানো যায় না। তার বড় কারণ এই এগিয়ে যাওয়ার পথে, মানুষ অনেক কিছু অর্জনও করেছে, যা তার অবস্থানকে গুণগতভাবে পাল্টে দিয়েছে। এমন বৈজ্ঞানিক সত্য ও জ্ঞান মানুষ লাভ করছে। যাতে ঐ ঈশ্বরের ও ধর্মের কোন স্থান নেই, প্রয়োজন হয়ে পড়েছে নতুনতর মূল্যবোধের, যার একমাত্র ভিত্তি মনুষ্যত্ব। এমন উৎপাদন পদ্ধতি মানুষ করায়ত্ত করছে, যাতে পুঁজিবাদের প্রাথমিক রূপ একেবারেই বেমানান ও বর্তমান স্তরও একসময়ে বিধ্বংসী হয়ে উঠছে। তাই প্রয়োজন নতুনতর এক ব্যবস্থা, যার প্রধান লক্ষ্য স্বনির্ভরতার নামে সংকীর্ণ জাতীয়তা নয়, ব্যাপক আস্তর্জাতিক সহযোগিতায় এক বিপুল গণ উৎপাদন ব্যবস্থা, যাতে পৃথিবীর সব মানুষ প্রায় সমান স্বাচ্ছন্দ্যে সুন্দর হয়ে উঠবে। কিন্তু এই প্রয়োজন কবে মিটবে তা জানা নেই,—হয়তো দু’ চার দশক বা দু’ চার শতাব্দী পরে। কিংবা হয়তো আদৌ মিটবে না, যদি মৌলবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদকে সক্রিয়ভাবে দ্রুততর না করা হয়; হয়তো তাহলে এই প্রয়োজন মেটার আগেই মৌলবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ, এই দুই দৈত্যের হাতে মানবসভ্যতার ধ্বংস ঘটবে (সেই সঙ্গে তাদেরও)। যাদের জন্য এই প্রয়োজন মেটার প্রয়োজন ছিল, সেই মানুষই আর থাকবে না।
এই ভয়ংকর পরিণতির কথা ভেবে আমরা শিহরিত হতে চাইনা। মানুষ বিপুল ক্ষমতাধর। তার মানবিকতা অক্ষয়, অমর। মৌলবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়ায় চরমতম সর্বনাশের প্রাগমুহূর্তেও সে রুখে দাঁড়াতে সক্ষম। এবং সে রুখে দাঁড়াবেও, দাঁড়াচ্ছেও।
—————————-
(১) অবশ্য এদের ‘অবতারত্ব সম্পর্কিত প্রচার ও বিশ্বাসও এক্ষেত্রে কিছুটা ভূমিকা পালন করে।
(২) হিন্দুদের মত বা মুসলিমদের নামাজের সময়ের মত মধ্যযুগে খৃস্টান ইয়োরোপেদিনে ৭টি বিশেষ ধর্মীয় সময় চিহ্নিত করা হত-(১) ম্যাটুটিনা-ব্রাহ্মা মুহূর্ত (বিছানা ছেড়ে ওঠার সময়), (২) প্রাইমা-সূর্যোদয় (৩) টার্সিয়া—সূর্যোদয় ও মধ্যাহ্নের মাঝামাঝি, (৪) সেক্ষ্ট্ৰী-মধ্যাহ্ব, (৫) নোনা-মধ্য অপরাহ্ন, (৬) ভেসপেরি—সূর্যাস্তের এক ঘণ্টা আগে, (৭) কমপ্লিাটা-সূর্যস্ত। এই সময়গুলিতে গীর্জা থেকে ঘন্টাধ্বনি করে সবাইকে জানানো হত।
(৩) তবে বিশেষ সময়ে কৌশল হিসেবে তারা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার কথাও বলে। যেমন, ‘সাম্রাজ্যবাদ রাখতে বিজেপি সঙ্গে চায় বাম দলগুলিকে—দলের সাধারণ সম্পাদক কে এন গোবিন্দাচাৰ্য আজ সরাসরি বামন্দালগুলিকে বলেছেন, বিজেপি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাও সংস্কার ঝেড়ে ফেলেনিয়া সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমরা একত্রে রুখে দাঁড়াই আসুন…’ ইত্যাদি। ব্যাপারটি প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা ও গণসমর্থন আদায় করা ইত্যাদির লক্ষ্যে একটি কৌশলীই ব্যাপারটি স্পষ্ট হয় যখন দেখা যায়। তার পরেই গোবিন্দাচাৰ্য বলেন, ‘আমাদের উচিত একজোট হয়ে ভারতীয় জীবনদর্শন ও মূল্যবোধকে রক্ষা করা।’ এই দর্শন ও মূল্যবোধ তাঁদের কাছে দ্বিধাহীনভাবে হিন্দুত্বেরই। (সংবাদ প্রতিদিন, ২৯.৯.৯৪)
(৪) কিন্তু শুরুতে পুঁজিবাদী বিকাশের জন্য প্রয়োজন ছিল বিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা। তখন এই ধর্মমোহ তার বিকাশে বিরোধী ভূমিকা পালন করছে বলে অনুভব করা গিয়েছিল। তাই শুরুর দিকে বুর্জেয়ারা ছিলেন ধর্মবিরোধী।
৬. মৌলবাদের সমাধান সন্ধানে
প্রথমেই স্বীকার করে নেওয়া ভাল, মৌলবাদী সমস্যার সমাধানে কোন চটজলদি ফর্মুলা বা প্রেসক্রিপশান হাতের কাছে মজুত নেই। আর এ ব্যাপারে নিজের বোধ এত কম ও অক্ষমতা এত বেশি যে, এ ধরনের কথা বলাও অনেকের কাছে একটি হাস্যকর ঔদ্ধত্য বলে মনে হতেই পারে। এ ব্যাপারে উপযুক্ত পণ্ডিত ও সচেতন ব্যক্তিরাও চিন্তাভাবনা করছেন। তাঁদের চিন্তার সামান্য শরিক হতে চাওয়াটা অন্যায় নয় বলেই, এমন ঔদ্ধত্য প্রকাশ করার সাহস হয়।
মৌলবাদী সমস্যার সমাধানের কথা ভাবতে গিয়ে প্রথমে একটি কথা মনে আসে যে, আদৌ এর সমাধানের প্রয়োজন আছে কিনা এবং যে ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে তার সৃষ্টি হয়েছে তাকে পরিবর্তন করাও সম্ভব কিনা। মৌলবাদের উচ্ছেদ ঘটানোটা যে অতি জরুরী তা হয়তো যে কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন, মানবতাবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিই নিদ্বিধায় স্বীকার করবেন। তবু প্রশ্ন জাগে, পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন ধর্মের মৌলবাদীরা ও সামগ্রিক ভাবে মৌলবাদী মানসিকতা যে জনসমর্থন বিগত দু’এক দশকের মধ্যে অর্জন করেছে, সেটি এটি অন্তত প্রমাণ করে যে, জনগণের একটি অংশ মৌলবাদ চান, হয়তো বা অসচেতনভাবে কিংবা ধর্মীয় অভ্যাসে। তাই তাঁদের এই আকাঙ্ক্ষাকে মর্যাদা না দেওয়া অনুচিত কিনা। একইভাবে সাম্রাজ্যবাদের জনবিরোধী ও মানবতাবিরোদী ভূমিকার কথা যাঁরা উপলব্ধি করেন, তাদেরও এই প্রশ্ন করা যায় যে, সত্যিই এইভাবে সাম্রাজ্যবাদকে চিহ্নিত করা উচিত হচ্ছে কিনা,–নাকি এটি একটি বিশেষ উৎপাদন ব্যবস্থার বিকশিত এক রূপ, যার সাহায্যে উৎপাদন বাড়ছে, বহু ভোগ্যপণ্যের সৃষ্টি হচ্ছে, বহু মানুষ এর ফলে সুখস্বচ্ছন্দ্যের মুখ দেখছেন (সাময়িকভাবে হলেও) এবং বহু মানুষ মানসিকঅর্থনৈতিক-সামাজিক ভাবে এই ব্যবস্থার শরিক হয়েছেন,-ধর্মবিশ্বাস তথা ধর্মের বিভিন্ন স্তরের শরিক হওয়ার মত।
মৌলবাদী মানসিকতায় অভ্যস্ত বা সাম্রাজ্যবাদের প্রসাদপুষ্ট মানুষদের কাছ থেকে এমন ধরনের কূট বিতর্ক উঠলেও উঠতে পারে, কিন্তু তা উভয়ের সভ্যতাবিরোধী ভূমিকাকে আলোকোজ্জ্বল আদৌ করে না। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এক সময়ে ইটালিতে ফ্যাসিবাদের অনুগামীও কম ছিল না। এই শতাব্দীর চতুর্থ দশকে যখন জার্মানীতে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সমগ্র জার্মান জাতিই তার সমর্থক ছিল, এবং এখনো তার অবশেষ আছে, নিও-নাৎসি গোষ্ঠী আছে, আছে একই ধরনের সন্ত্রাসবাদী কর্তৃত্ববাদ ও হিংস্র৷ জাতীয়তাবোধ। তবু দক্ষিণপাহী-বামপন্থী নির্বিশেষে পৃথিবীর কোন শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষই তার উৎসাহদাতার ভূমিকা পালন করতে ইচ্ছুক নন। কারণ ফ্যাসিবাদকে ‘ফ্যাইন্যান্স পুঁজির সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল একনায়কত্ব’ হিসেবে অনুভব করা যাক বা না যাক, এটি অন্তত বোঝা গেছে কি বীভৎস নারকীয়তার সঙ্গে সে তার কাজ হাসিল করতে চায়, কিভাবে বাজারের স্বার্থে যুদ্ধ বাধায়, কিভাবে লক্ষ লক্ষ নির্দোষ আবালবৃদ্ধবনিতাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এই মানবতাবিরোধী মানসিকতার অবসানে তাই দলমত নির্বিশেষে বহু মানুষ এক সময় সংগ্ৰাম করেছেন। ১৯৪৫– এ, এখন থেকে ৫০ বছর আগে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়েছিল। কিন্তু ঐ ফ্যাসিবাদ ভিন্ন রূপে এখনো আছে, রেখে গেছে তার সঙ্গীসাথী ও সন্তানসন্ততিদের। এদেরই অন্যতম ধর্মীয় মৌলবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ।
পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা মানুষের সমস্যা সমাধানের কোন পথ যে আদৌ নয়, তা বোঝা যায় তাদের নিজেদেরই ক্রমবর্ধমান সংকটের বিপুলতা থেকে। এই ব্যবস্থা নৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক সংকটে ক্রমশ নিমজমান। নৈতিকসামাজিক ক্ষেত্রে সংকট ও অবক্ষয় কি ভয়াবহতা অর্জন করেছে তা উন্নত ইংরেজ জাতির’ সাম্প্রতিক অবস্থা থেকে আচি করা যেতে পারে; শুধু বিগত ২৫ বছরে (১৯৭০-৯৫) ইংল্যান্ডের এই অবস্থা কেমন দাঁড়িয়েছে তার একটি আংশিক চিত্র শ্ৰী নীরদচন্দ্ৰ চৌধুরীর বর্ণনা থেকে পাওয়া যেতে পারে।–
‘১. নরনারী সম্পর্কিত আচরণ। বর্তমানে ইংরেজের মধ্যে লাম্পট্যের যে বিস্তার, বর্বরতা এবং নিষ্ঠুরতা দেখা যাইতেছে তাহা দ্বিতীয় চার্লস-এর যুগে বা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষেও দেখা যায় নাই।
এ-যুগের ইংরেজ লম্পটেরা শিশু, বালিকা ও বৃদ্ধাকেও বলাৎকার করিয়া হত্যা করিতেছে। এমন কি বারো তেরো বৎসরের বালকও এইরূপ বলাৎকার করিতেছে। অপর পক্ষে অল্পবয়স্কপ বালিকারাও এরূপ কামপরবশ হইয়াছে যে, তাহাদিগকে গৰ্ভ নিবারণের ঔষধ দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।
২। নরহত্যা। শুধু কামের বশেই নয়, অর্থের জন্যও নরহত্যার বিস্তার হইতেছে। বারো-তেরো বৎসরের বালকেরাও সামান্য অর্থের জন্য পেনসনভোগিনী বৃদ্ধাকে হত্যা করিতেছে। আমি ১৯৭৫ সাল পর্যন্তও অক্সফোর্ডের চারিদিকে অতি নির্জন স্থানে প্রাতঃভ্রমণ করিতে যাইতাম, এখন আর ভরসা পাইনা।
৩। গুন্ডাবাজির যে প্রসার হইয়াছে, উহা ভীতিজনক, একটু রাগ হইলেই একজন বা একদল অন্য ব্যক্তির বা অন্য দলের উপর ছোরা চালাইতেছে।
৪। অর্থালিন্সা সর্বব্যাপী এবং সকল বয়সের ইংরেজের মধ্যে দেখা দিয়াছে, কিন্তু সেই অৰ্থলিন্সাও, লাম্পট্যের মতই, ইতর, সামান্য অর্থের জন্য। সকল ইংরেজের মনে এক চিন্তা-কি করিয়া টাকা হইবে-ইংরেজি ভাষায় উহার পরিচয় দিতে হইলে বলিতে হয়–Everybody wants his penny-worth for his penny or his penny for his pennyworth. ইহার বেশি উচ্চ ধারণা অর্থোপার্জন সম্বন্ধেও নাই।’ (দেশ; ১২.৮.৯৫)
যাঁরা একটু খোঁজ খবর রাখেন তাঁরা জানেন আমেরিকা ও তার মানুষও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। ‘ইউ এস নিউজ অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড রিপোর্ট নামে মার্কিন সাময়িকী ১৯৮০-তে এ ব্যাপারে যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছিল তার থেকে জানা যায়, ওখানে ‘গড়ে প্রতি দু সেকেন্ডে একটি সিঁদেল চুরি, প্রতি ২৮ সেকেন্ডে একটি গাড়ি চুরি, প্রতি ৪৮ সেকেন্ডে একটি মারাত্মক শারীরিক আক্রমণ ও আঘাত, প্রতি ৫৮ সেকেন্ডে একটি সশস্ত্ৰ ডাকাতি, প্রতি ৬ মিনিটে একটি ধর্ষণ এবং প্রতি ২৩ মিনিটে একটি খুনের ঘটনা ঘটে।’ এবং সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান এর চেয়ে আশাব্যঞ্জক তো নয়ই, বরং আরো ভয়াবহ।
নৈতিক ও সামাজিক এই সংকট যে ধর্মহীনতার জন্য সৃষ্টি হয়েছে তা আদৌ নয়। ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় প্রতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রভাব ও ধর্মবিশ্বাস যথেষ্টই আছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিপুলভাবে এগিয়ে থাকলেও এই এগিয়ে থাকার ব্যাপারটি নিছকই যান্ত্রিক ও শ্রেণী:স্বার্থে প্রযুক্ত। প্রকৃত বিজ্ঞানমনস্কতার পরিবেশ এমন পুঁজিবাদী তথা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিতে এখনো তৈরি হয় নি। এরই একটি প্রতিফলন ঘটে এমন দেশের নাগরিকদের মধ্যে ঈশ্বরবিশ্বাস ও ধর্মমোহ থেকে মুক্তির মানসিকতা অতি নূ্যনতমমাত্রায় বিকশিত হওয়ার মধ্যে। যেমন ১৯৮০ সালের হিসাব অনুযায়ী উত্তর কোরিয়ার শতকরা ৬৭.৯ জন, আলবেনিয়ার ৫৫.৪ জন, চীনের ৭১.২ জন বা মঙ্গোলিয়ার ৬৫.৪ জন (১৯৯০) ব্যক্তি যখন ঈশ্বরবিশ্বাসমুক্ত (atheist) ও ধর্ম-পরিচয়হীন (nonreligious) হিসাবে নিজেদের ঘোষণা করেছেন, সেখানে আমেরিকায় এমন মানুষের সংখ্যা মাত্র শতকরা ৬.৮ ও ইংল্যান্ডে ৮.৮ ভাগ। (বিগত বছরগুলিতে এই পরিসংখ্যান বিরাটভাবে কিছু পরিবর্তিত হয় নি।) স্পষ্টতঃই আমেরিকা বা ইংল্যান্ডের ৯০ ভাগেরও বেশি মানুষ ধর্ম ও ঈশ্বরকে যতটুকুই হোক না কেন এবং যেভাবেই হোক না কেন আঁকড়ে আছেন। আমেরিকায় ফান্ডামেন্টালিজমসহ চার্চের প্রভাব কম নয়। ইংল্যান্ডে তো রাজতন্ত্রের পাশাপাশি চার্চ অব ইংল্যান্ড-স্কটল্যান্ডের মহিমা ও প্রাধান্য বিপুল। এই অবস্থায় ইংল্যান্ডে বা আমেরিকায় এই চূড়ান্ত নৈতিক অবক্ষয়, এই হিংস্রতা, লাম্পট্য ও অর্থগৃধুতা, চরম ভোগবাদী মানসিকতার পেছনে বস্তুবাদী দর্শনের বা বামপন্থী আন্দোলনের ভূমিকা শূন্য। বরং এটি বলা অসঙ্গত নয় যে, এর পেছনে ভূমিকা পালন করেছে। ধর্ম এবং শোষণভিত্তিক পুঁজিবাদী তথা সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার ককটেল। খৃস্ট ধর্মের ব্যবহার ঐ সব দেশে সম্পূর্ণত আদর্শ মৌলবাদী চরিত্র হয়তো অর্জন করে নি। কিন্তু মানসিকতা বা ভিত্তি আছেই, এবং ঐসব দেশে হিংস্র ধর্মীয় মৌলবাদের অনুপস্থিতির একটি বড় কারণ হিংস্র ভিন্ন বা বিরোধী ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির সংখ্যার নূ্যনতম পরিমাণ। (আমেরিকায় শতকরা মাত্র ৬.৭ জন ও ইংল্যান্ডে শতকরা ৪.৩ জন ব্যক্তি অন্যান্য নানা ধর্মাবলম্বী।)
এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, আমেরিকা-ইংল্যান্ডের মত দেশগুলির ধর্ম ও পুঁজিবাদী সংস্কৃতির ককটেল ভারতের মত দেশেও চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে এবং সম্প্রতি তা বিপুল উদ্যোগে বাড়ানো হচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে ‘সর্বধর্মে সমভাব’ করে ধর্মীয় সুড়সুড়ি দেওয়া হয়েছে, ধর্মীয় মৌলবাদের সৃষ্টির পথ পরিষ্কার করা হয়েছে। বামপন্থী-দক্ষিণপন্থী নির্বিশেষে প্রায় সব রাজনৈতিক সুবিধাবাদী দলগুলি ভোটের লক্ষ্যে ধর্মীয় কুসংস্কার এবং ধর্মকে ব্যবহার করছে ও প্রশ্ৰয় দিচ্ছে। অন্যদিকে-ভোগবাদ, পণ্যবাদ বা কনজিউমারজম, আত্মকেন্দ্রিকতা, যে কোনভাবে অর্থোপার্জনের মানসিকতা ইত্যাদি এবং এসবকে জনপ্রিয় করার জন্য যৌনতা ও হিংস্রতার সংস্কৃতি–কে দূরদর্শন ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে ঢালাও ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে। সবাইকে নিয়ে বাঁচা নয়, শুধু নিজেকে প্রতিষ্ঠা করাই এখনকার যুব সমাজের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে।
(সামাজিকভাবে এর প্রতিফলনও ঘটছে। এর একটি সামান্য পরিচয় এ ধরনের হিসাব থেকে পাওয়া যাবে যে, ভারতে এখন প্ৰতি ৪৭ মিনিটে একজন নারী ধর্ষিতা হন, প্ৰতি ৪৪ মিনিটে একজন নারী অপহৃত হন এবং প্রতিদিন পণজনিত কারণে বধূহত্যা ঘটে ১৭টি। —-গণশক্তি, ৬৯.৯৫)
আমেরিকা-ইংল্যান্ডে ধর্মের অবস্থান থেকে এটি বোঝা যায় যে, ধর্ম এই নৈতিক সংকট আটকানোর ক্ষেত্রে কোন ভূমিকা তো নেয়ই না, বরং তাকে বাড়িয়ে তোলায় সাহায্য করে। কোন কোন সরল বিশ্বাসী ধামিক ব্যক্তি এমন মনে করতে পারেন যে, ধর্মের মূল শিক্ষা ঐ সব দেশের মানুষ ভুলে গেছে, আগে এই শিক্ষা ছিল বলে এমন নৈতিক-সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টি হয় নি। এটি একটি ভ্রান্ত ও আত্মপ্রবঞ্চনাকারী ধারণা। অতীতেও, ধর্মীয় শিক্ষার চেয়ে, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও ঐ অনুযায়ী সামাজিক পরিকাঠামোই। এ ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেছে। যে ব্যবস্থায় বর্তমানের পুঁজিবাদী তথা সাম্রাজ্যবাদী পরিকাঠামো টিকিয়ে রাখার উপযোগী মুনাফা বাড়ানো, পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবর্তে অবাধ প্রতিযোগিতা (অর্থাৎ অন্যকে ল্যাং মেরে বা ধাক্কা মেরেও নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া), চূড়ান্ত পণ্য নির্ভরতা, ক্রমবর্ধমান ভোগবাদ (না হলে পণ্য বিক্রি হবে না) ইত্যাদি থাকার প্রয়োজন ছিল না বা থাকবে না সেই ব্যবস্থাগুলিতে এমন অর্ধগৃধুতা, হিংস্ৰতা ও তাদের হাত ধরাধরি করে আসা যৌনবিকৃতি সৃষ্টির পরিবেশও শক্তিশালী ছিল না বা থাকবে না। বরং দেখা গেছে তথাকথিক ধৰ্মশাস্ত্রগুলিতে আদিম যৌনতাকে সুড়সুড়ি দেওয়ার উপকরণ বহুতু পরিমাণেই মজুত আছে। ‘লীলা’ বলে যতই চালানোর চেষ্টা করা হোক না কেন, শ্ৰীকৃষ্ণের উলঙ্গ গোপিনীদের তারিয়ে তারিয়ে দেখার, বা ছদ্মবেশে ঝোপে ঝাড়ে কুয়াশার মধ্যে যেখানেই হোক সুন্দরী মহিলাদের উপর হামলে পড়ার দৈব অনুগ্রহের’ মত অজস্র লাম্পট্যের ঘটনা এই সব তথাকথিত ধর্মগ্রন্থে অসংখ্য রয়েছে। আছে শ্ৰীীরামচন্দ্রের সুগ্ৰীব বধ বা ইন্দ্ৰজিতকে খুন করার মত নৃশংস হিংস্রতার অজস্র উদাহরণও। ব্যাপারগুলি তখনকার পরিবেশে স্বাভাবিক হয়তো ছিল। কিন্তু ধর্মের নামে এখনো তা প্রচার করা ও মহীয়ান করার অর্থ ঐ বিকৃতিকে, ক্যান্সার বৃদ্ধিকারী উত্তেজনার (carcinogenic) ভূমিকা নিয়ে বাড়িয়ে তোলা। সাম্রাজ্যবাদী সংস্কৃতিও তাই চায়। তারা চায় ধর্মের অবৈজ্ঞানিক মানসিকতার সঙ্গে যৌনতায় আচ্ছন্ন এক ব্যক্তিত্বহীন ক্ৰেতাজনগণ, যারা যা প্রচার করা হবে। বিনাযুক্তি প্রয়োগে (যেন ঈশ্বরভক্তির মত), নিজেকে তৃপ্ত করতে (যেন এক যৌন আনন্দ লাভের মত) তাই-ই কিনবে।
মৌলবাদী ধর্মের এই নোংরা ব্যবহারের এক কেন্দ্রীভূত রূপ,—তার এই কেন্দ্রীভবন মূলত ধর্মকে নিয়ে, সাম্রাজ্যবাদের কেন্দ্রীভবন যেমন ঘটে একচেটিয়া পুঁজির মধ্যে। সাম্রাজ্যবাদ সামান্য সংখ্যক কিছু মানুষের একটি ছোট্ট গোষ্ঠীর স্বাের্থরক্ষণ করতে, বিপুল সংখ্যক পৃথিবীবাসীকে তাদের অর্থনৈতিকভাবে ক্রীতদাস, সাংস্কৃতিকভাবে পঙ্গু এক সত্তায় পরিণত করতে চায়। ধর্মীয় মৌলবাদও তেমনি মানুষকে এক ভাববাদী অবৈজ্ঞানিক চেতনার ক্রীতদাসে পরিণত করতে ও স্বাধীন বিকাশে অক্ষম, জড়বদ্ধ প্রাচীন সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে আচ্ছন্ন করে পঙ্গু করে তুলতে চায়। উভয়ের নেতৃত্ব দেয় স্বল্প কিছু মানুষের একটি আপাত শক্তিশালী শ্রেণী, যারা বিপুল শক্তিধর ব্যাপক সংখ্যক মানুষকে সাময়িকভাবে শাসন করে বা করতে চায়। তাই উভয়েই সমানভাবে ঘূণ্য, পরিত্যাজ্য ও মানবতার শত্রু।
এরা মানুষের স্বাভাবিক মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করে। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতাই ভালবাসা ও পরস্পরকে সাহায্য করা। এর পেছনে তার হরমোন ও জীন-গত (genetic) গঠন যেমন কাজ করে, তেমনি কাজ করে তার বহু শত বছরের অভিজ্ঞতা, যে অভিজ্ঞতায় সে জেনেছে পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া প্রতিকূল পরিবেশে টিকে থাকা সম্ভব নয়। ফ্যাসিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ধর্মীয় মৌলবাদ—একই বৃন্তের এই তিন বিষফুল মানুষের এই পারস্পরিক মমত্ববোধ, সহযোগিতা ও সহমর্মিতাকে ধ্বংস করতে চায়। তা না করলে তাদের অস্তিত্বই সম্ভব নয়।
জার্মানির সেই ফ্যাসিবাদ শুধু বাঁচার কথা বলেছিল জার্মান জাতিকে,-ইহুদি ও অন্যান্য তথাকথিত অনার্যদের শত্রু বলে বিপুল সংখ্যক জার্মান নাগরিককে বিশ্বাস করিয়েছিল। এটি বৃহদংশ জার্মানদের কাছে জনপ্রিয়ও হয়েছিল; তেমনি তা বৃহত্তর মানবিক ঐক্য, সৌহার্দ ও সম্প্রীতিকে ধ্বংস করে অন্যের প্রতি ঘৃণা ও নির্মম হিংস্রতার বহিঃপ্রকাশও ঘটিয়েছিল। এটিকে শুধু পাশবিক বল্লে, পশুদেরও অপমান করা হয়, কারণ এটি জানা আছে যে আত্মরক্ষা, প্রাণধারণের জন্য খাদ্যে টান পড়া, যৌন অতৃপ্তি ইত্যাদির চরম প্রয়োজন ছাড়া সাধারণতঃ পশুরাও পরস্পরের প্রতিহিংস্র হয়ে ওঠে না। এখন সাম্রাজ্যবাদ প্রায়শঃ আরো ঠাণ্ডা মাথায় এ কাজ করে। হিটলারি-উগ্রতার ও চটজলদি সব কিছু পাওয়ার ততটা প্রয়োজন তার সবসময় হয় না, যতটা প্রয়োজন হয় ধীরগতিতে বিপুল সংখ্যক মানুষের সাংস্কৃতিক চেতনা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং অর্থনীতি ও সমাজকে নিজের কন্তুজায় আনতে। এর ফলেই সে অন্যদের শুধু নিজের প্রতিযোগী হিসেবে ভাবতে শেখায়, সহযোগী বা সাখী হিসেবে নয়। কিভাবে প্রতিযোগিতায় ব্যবসা ও পুঁজি বাড়বে, নিজের ভাল চাকরি ও পদ অর্জন করা সম্ভব হবে, অর্থদায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র হওয়া যাবে-এই ই তার শিক্ষণীয়। যতদিন এই ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখা হবে, এমনকি তার শ্ৰীবৃদ্ধিও ঘটানো হবে, ততদিন মানুষে মানুষে সত্যিকারের সম্প্রীতি ও সহযোগিতার বাতাবরণ গড়ে তোলা সম্ভব নয়। আর এই প্রতিযোগিতার ব্যাপকতর প্রয়োগ ঘটে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দাঙ্গা সৃষ্টির মধ্যে, বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে মদত দেওয়ার মধ্যে—যে সবগুলিতে মাঝখান থেকে মারা পড়ে নিরীহ শতশত মানুষ, নিরপরাধ অসহায় মানুষই। যেন এক অদৃশ্য সুতোর টানে তারা মৃত্যুমুখে এগিয়ে যায়।
ধর্মীয় মৌলবাদ (এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদও) ধর্মকে কেন্দ্র করে এই মানবিক অনৈক্য প্রতিষ্ঠা করতে ও প্ৰেমগ্ৰীতিহীন ফ্যাসিস্ট ধর্মীয় সত্তা গড়ে তুলতে চায়। একদা যেসব প্রতিবেশীরা ধর্মবিশ্বাস নির্বিশেষে দীর্ঘকাল পরস্পরের সহযোগী সুহৃদ হয়ে বেঁচেছিল, তারা এক সময় এই ধৰ্মীয় অপশক্তির হাতে ধরা সুতোর টানে ছুরি হাতে পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মানুষ থেকে অমানুষ হয় ওঠে। নবজাত শিশুদের শরীরে শারীরিক চিহ্ন হিসেবে কোন ধর্ম নেই, জাত নেই, শ্রেণী নেই। সমাজই তাকে এক সময় এমনভাবে শিক্ষিত করে ও এমন পরিচয়ে পরিচিত করায়। এই কৃত্রিম পরিচয় ও বিভাজন ধর্মের একটি কাজ। ধর্মীয় মৌলবাদ এই বিভাজনকে বাহ্যিক নয়। অভ্যন্তরীণ, পরিবর্তনীয় নয় অপরিবর্তনীয় ও অলঙঘ্য হিসেবে সুতীব্রভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এ করতে গিয়ে সে ভিন্ন ধর্মের প্রতিবেশী মানুষদের প্রতিযোগী হিসেবে ও সমস্যার কারণ হিসেবে, এমনকি দেশেরও শত্ৰু হিসেবে চিহ্নিত করে। (ভাষাগত, জাতিগত, অঞ্চলগত ইত্যাদি ধরনের সাম্প্রদায়িকতাবাদীরাও তাই-ই করে।) সংখ্যায় যারা যেখানে বেশি সেখানে তারা ছড়ি চালায়। তার প্রতিক্রিয়ায় সংখ্যালঘুরাও ছড়ি ধরে। বিভাজন, অপ্রেম, অবিশ্বাস বেড়েই চলে। মৌলবাদকে ও সাম্প্রদায়িকতাকে টিকিয়ে রাখা ও বাড়তে দেওয়ার অর্থ মানুষের স্বভাববিরোধী এই সব দিকগুলিকে দ্রুত বাড়িয়ে তোলা, যার পরিণতি দাঙ্গা, যুদ্ধ ও ধ্বংসই হতে বাধ্য। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে বিশেষ ধর্মের মানুয নিজেদের কিছুদিনের জন্য শক্তিশালী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে ও কর্তৃত্বলাভ করতে পারে, কিন্তু দীর্ঘকাল নয়। ভিন্ন গোষ্ঠীর যাদের সে শত্রু পরিণত করেছে, হত্যা করেছে, নিপীড়ন চালিয়েছে তারা প্ৰতিশোধ নোবেই। অবিশ্বাস ও শক্রিতার পথ ধরে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে আসবে এই পারস্পরিক হনন, যদি না মানুষের শুভবুদ্ধি এই চক্রকে মধ্যপথে ছিন্ন করে। এবং তা করেও।
রাজনৈতিক মৌলবাদও দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষার নামে ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশ, স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ও বিশেষ ভাললাগা-মন্দলাগার বোধ আর আবেগগুলিকে অস্বীকার করে। এবং পদদলিত করে,—এক রাজনৈতিক কর্তৃত্বের (তা ব্যক্তির বা গ্রন্থের) অধীনে। ‘রোবট’-এ পরিণত করে তার অনুগতদের। অন্যদিকে এই মানসিকতা ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের জনসাধারণকে শত্রু (শ্রেণীশত্রু?) হিসেবে, প্রতিযোগী হিসেবে ও সহযোগিতা পাওয়ার অযোগ্য বলে প্রতিষ্ঠা করে। একদা যে জনগণ বন্ধুর মত দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস করেছে, এখন রাজনৈতিক সচেতনতার নামে পাটিপরিচয় পরস্পরের মধ্যে বিভেদ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করছে। এমনকি আমাদের মত দেশের গ্রামেগঞ্জেও, আগের মত ‘কৌন জাত বা’-র পরিবর্তে ‘কৌন পাটি বা’—এ প্রশ্নই সামনে আসে। ব্যাপারটি ধর্মীয় বা জাতপাতের বিভাজনের চেয়ে সামান্য কিছুটা সুস্থতর মনে হলেও, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও অনৈক্য সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট। এর ফলে রাজনৈতিক হানাহানিই বাড়ে। সবাই জনগণের মঙ্গলের কথা বলে, কিন্তু সবাই জনগণকেই বলি দিতে থাকে। মতাদর্শের অনুদার, যান্ত্রিক ও অমানবিক প্রয়োগ এই মৌলবাদীদের,—তারা ধর্ম ও ধর্মীয় মৌলবাদ, এমন কি পুঁজিবাদসাম্রাজ্যবাদের বিরোধী ভূমিকা নিলেও, মূলবিচারে মানুষের শত্রুতে পরিণত করে। তাই সবধরনের মৌলবাদই যে পরিত্যাজ্য এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। রাজনৈতিক মৌলবাদী মানসিকতার সমাধান হয়তো ভবিষ্যতে কোনদিন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অবলুপ্তির মধ্য দিয়ে হতে পারে, যখন বৃহত্তর সমবায় ভিত্তিক ও নূ্যনতম কিছু ক্ষেত্রে ঐক্যভিত্তিক মতাদর্শ ও কর্মসূচীকে সামনে রেখে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবন, সমাজ ও সংস্কৃতিকে স্বচ্ছল ও সুস্থ করে তুলবে। কিন্তু এটি অর্জনের পূর্বশর্ত সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও ধর্মীয় বিভাজনকে ধ্বংস করা এবং সাম্রাজ্যবাদ ও ধর্মীয় মৌলবাদকে অবলুপ্ত করা। কারণ এই শোষণ ও এই বিভাজন এমন ঐক্যের ভিত্তিমূলের শত্ৰু, শেকড়েই তাকে বিনষ্ট করে দিতে সচেষ্ট। আর এই সাম্রাজ্যবাদ ও মৌলবাদের উচ্ছেদে পরস্পর সংযুক্ত দুটি মোটা দাগের দায়িত্বের কথা বলা যায়—তা হল সচেতনতা ও সংগ্রাম।
ধর্মীয় মৌলবাদ প্রসঙ্গে এই সচেতনতার লক্ষ্য,-ধর্ম ও ধর্মীয় মৌলবাদ সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত সত্যগুলিকে জানা, তার উদ্ভব ও সৃষ্টির ইতিহাস ও কারণগুলিকে উপলব্ধি করা। সংগ্রামের লক্ষ্য,-যে ব্যবস্থার উপরিকাঠামো হিসেবে ধর্ম ও ধর্মীয় মৌলবাদের টিকে থাকা ও সৃষ্টি হওয়া, সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন। এবং প্রয়োজনে ধর্মের বিরুদ্ধে সংগ্রামও।
বর্তমান পরিস্থিতিতে বিপুল সংখ্যক মানুষকে সচেতন করে তোলা একটি বড় প্রয়োজন। এর ফলে ধর্ম, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের শিকার তারা হবেন কি হবেন না, এই সিদ্ধান্ত র্তারা নিজেরাই নেওয়ার উপযুক্ত হয়ে উঠবেন। আর ফলতঃ পারস্পরিক হানাহানি বন্ধ করে প্রকৃতির বিরুদ্ধে ও অর্থনৈতিক সংগ্রামে যুক্ত হওয়াকে তাঁরা সুস্থতর ব্যাপার বলে অনুভব করতে সক্ষম হবেন।
ধর্মীয় মৌলবাদ সৃষ্টির পেছনে এই সংগ্রামের শূন্যতা একটি বড় ভূমিকা পালন করে। তাই তৃণমূল স্তর অব্দি বিস্তৃত বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে অবিজ্ঞান ও গণবিরোধী শত্রুর বিরুেদ্ধে সংগ্রাম যত বিস্তৃত হবে, ধর্মীয় মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতা ততই হ্রাস পাবে বা প্ৰতিহত হবে। এক্ষেত্রে সঠিক বামপন্থী আন্দোলনই তার গণমুখী, ভাববাদবিরোধী মতাদর্শ নিয়ে এবং অর্থনৈতিক ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামের পাশাপাশি একটি বিরাট ভূমিকা নিতে সক্ষম। এটি ঠিক যে, এই সঠিক’ কথাটি একটি বিরাট গোঁজামিলের ব্যাপার। চূড়ান্ত অর্থে সঠিক কোন কিছু সম্ভব নয়। তবু ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতাগুলিকে আন্তরিকভাবে ও খোলামনে নূ্যনতম করার মধ্য দিয়ে এই সঠিকতার কাছাকাছি পৌঁছনোর চেষ্টা করাটা অসম্ভব নয়।
ধর্মের প্রভাব মুক্ত এবং বিজ্ঞানমনস্ক মানসিকতার নেতৃত্বে, অজস্র সংগঠন গড়ে তোলা দরকার। দেশের প্রতিটি গ্রামে ও শহরের প্রতিটি পাড়ায় এ ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্থা বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। আন্তরিক ইচ্ছা থাকলে সরকারী উদ্যোগেই প্রতিটি গ্রামে ও পাড়ায় সামান্য কিছু সাম্মানিক দিয়ে দু’তিন জন স্থানীয় সচেতন তরুণ-তরুণীকে এ ব্যাপারে নিয়োগ করা যায় এবং পশ্চিমবঙ্গ এ ক্ষেত্রে একটি মডেল রাজ্য হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে। সাক্ষরতা কর্মসূচীর অঙ্গ হিসেবে এ রাজ্যে দু’একটি জেলায় এমন উদ্যোগ গড়েও উঠছে। (যেমন বর্ধমান জেলায় ১৯৯৫-এর অক্টোবরের সূর্যগ্রহণকে কেন্দ্র করে।) তবে এটি সভয়ে লক্ষ্য করার ব্যাপার যে, এই সুস্থ উদ্যোগ যেন সংকীর্ণ দলবাজির শিকার না হয় এবং দলীয় রাজনীতিকে বা তার মাহাত্ম্যকে প্রতিষ্ঠা করার আত্মহননকারী উদ্যোগে না পর্যবসিত হয়। এছাড়া এই পশ্চিমবঙ্গের (অন্যান্য কিছু রাজ্যেও)। সরকারী প্রভাবমুক্ত বহু বিজ্ঞানসংস্থা গড়ে উঠেছে। এদেরও গোঁড়ামিমুক্ত সামগ্রিক ঐক্যবদ্ধতা ধৰ্মীয় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা রুখতে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে সক্ষম এবং প্রকৃতপক্ষে সরকারীভাবে একাজ কতটা আন্তরিকভাবে হবে, এ ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহও আছে। এখনকার পরিস্থিতিতে সরকারী বন্ধন মুক্ত মানুষের গণ উদ্যোগ এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নিতে সক্ষম।
ধর্মীয় মৌলবাদ যেভাবে মাথা চাড়া দিচ্ছে, তাতে এ ধরনের গণবিজ্ঞান আন্দোলন অতি গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী। এক্ষেত্রে মৌলবাদবিরোধী প্রত্যেকের মধ্যে ও প্রতিটি সংস্থার মধ্যে ঐক্যও গুরুত্বপূর্ণ। সেক্ষেত্রে বুর্জেয়া নাস্তিকতা ও যান্ত্রিক যুক্তিবাদের সঙ্গে বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ হওয়াটাও দরকার। কি হিন্দু, কি ইসলাম, কি খৃস্ট–সব ধরনের ধর্মীয় মৌলবাদীরা ক্ষমতা পেলে পরিপূর্ণ ফ্যাসিবাদী ক্রিয়াকাণ্ড শুরু করার জন্য প্রস্তুত। শিবসেনা-আর এস এস-এর মত হিন্দু মৌলবাদী নয়াফ্যাসিস্ট গোষ্ঠী বা ইরান থেকে পাকিস্তান নানা দেশের অজস্র মুসলিম মৌলবাদী সংগঠনগুলি প্রকাশ্যে এমন কথাবার্তাও বলে এবং ফ্যাসিবাদের ইঙ্গিত দেয়। (নেহাত বি জে পি-র মত কিছু কিছু ‘রাজনৈতিক দল’ আইন বাঁচাতে ও ভোটে দাঁড়ানোর জন্য প্রকাশ্যে এখনকার মত একটু রেখে ঢেকে কথা বলে।) সেক্ষেত্রে এরা ক্ষমতা পেলে,-হিটলারের ইহুদি নিধনের মত, ভিন্ন ধর্মের এবং কম্যুনিষ্ট বা মুক্তমনানাস্তিক-ধর্মপরিচয়মুক্ত বলে মনে করা ব্যক্তিদের লাখে লাখে হত্যা করতে পিছপা হবে না।(১) (৯০ কোটি ভারতবাসীর ৮-১০ কোটিকে মেরে ফেল্পে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকেই যাবে।) হয় পরিপূর্ণ আনুগত্য, কিংবা নিশ্চিহ্নকরণ—এই এদের নীতি। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি আটকাতে ধর্মীয় মৌলবাদীদের সামান্য সংস্রবকেই প্রধান গুরুত্ব দিয়ে প্রতিহত করার কাজে সামান্যতম গাফিলতির কোন ক্ষমা নেই। মৌলবাদী প্রভাব ও প্রচার টিকিয়ে রাখার অর্থ অন্যান্য ক্ষতির পাশাপাশি এই লক্ষ্যে তাদের পৌঁছনোর পথকে খুলে রাখা।
সমাজের শ্রেণীবিভাজন ও শ্রেণীবৈষম্যকে স্বীকার করুন, বা না করুন, অন্তত ধর্মীয় প্রভাব তথা ধর্মীয় মৌলবাদের প্রভাবকে আটকানোর প্রশ্নে, তাই ধর্মনিরপেক্ষ বুর্জেয়া, বুর্জেয়া নাস্তিক ও যুক্তিবাদীদের সঙ্গে বামপহী-দক্ষিণপন্থী নির্বিশেষে সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক গোষ্ঠীরও যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলা এবং ঐক্যবদ্ধ ব্যাপক কর্মসূচী নেওয়া উচিত। এঁরা পরস্পরের মধ্যে রাজনৈতিক সংগ্ৰাম চালাতেই পারেন, কিন্তু মৌলবাদ বিরোধিতার প্রশ্নে নিজেদের অনৈক্য মৌলবাদের আগমনকেই উৎসাহিত করবে।
নিজেদের ও প্রতিবেশীদের,-বিশেষত দরিদ্র, প্রথাগত শিক্ষাবর্জিত ও সামাজিকভাবে অবহেলিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে, সচেতনতা বৃদ্ধির ঐক্যবদ্ধ ও গণমুখী ব্যাপক বিজ্ঞান আন্দোলন, কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা বিরোধী কাজকর্ম এবং সরাসরি মৌলবাদবিরোধিতা তীব্রতম করার সময় এসেছে। নিছক বিজ্ঞান আন্দোলনের জন্য বিজ্ঞান আন্দোলনও এ ক্ষেত্রে কিছু ভূমিকা রাখবেই। কিন্তু সচেতন ব্যক্তিদের উচিত এই বিজ্ঞান আন্দোলনকে সমস্ত ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলন, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন এবং ছাত্র-যুব-নারী সংগঠনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। এবং উচিত ক্রমশ এই বিজ্ঞান আন্দোলনকে শ্রেণী সচেতনতা ও সমাজঅর্থনীতি সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক উপলব্ধির দিকে নিয়ে যাওয়া। যান্ত্রিক যুক্তিবাদী ক্রিয়াকাণ্ড বা শ্রেণীবোধহীন বুর্জেয়া নাস্তিকতা আমাদের মত বিপুল সংখ্যক দরিদ্র ও নিরক্ষর জনসাধারণের দেশে একটি স্তর আদি মূল্যবান হলেও, ক্রমশঃ যদি না তার এই উত্তরণ ঘটানো যায়। তবে তা একসময় কানাগলির সম্মুখীন হতে ও ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই উত্তরণের অভাবে এই ধরনের যান্ত্রিক বিজ্ঞান আন্দোলন এক সময় মৌলবাদের মত সামাজিক অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হতে থাকে এবং দোদুল্যমান শিক্ষিত মানুষ (এমনকি তথাকথিত বিজ্ঞানীদের’ও) সৃষ্টি করে, যারা সুযোগ পেলেই অবিজ্ঞান, ধর্মীয় কুসংস্কার এমনকি ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের শিকার হয়ে যায়। এই উত্তরণের অভাবেই যান্ত্রিক যুক্তিবাদী আন্দোলনের মধ্যে স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্বের সৃষ্টি হয়, যে নিজেকে নির্ভুল সবোত্তম বলে ভাবে, ভিন্ন গোষ্ঠীর লোকেদের শত্রু বলে ধরে নেয় এবং মানুষের অজ্ঞতা, কুসংস্কার ও অনাবিল ধর্মবিশ্বাসকে অপমান ও ব্যঙ্গ করে। বিজ্ঞান আন্দোলনের মূল লক্ষ্য বিজ্ঞানমনস্কতা অর্জন করা, যার সাহায্যে ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি সম্পর্কে তথা মানুষের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাজন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান ক্রমশ উচ্চ পরিমাণে লাভ করা সম্ভব। এর ফলেই একজন বিনয়ী, পরমতসহিষ্ণু, মানবিকও হয়ে ওঠে। কারণ প্রকৃত বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিই ক্ৰমশঃ উপলব্ধি করতে পারেন জ্ঞান কত বিপুল। আর ব্যক্তিগতভাবে তার কত ক্ষুদ্র অংশ জানা সম্ভব এবং জ্ঞানের চরম সত্যতা, কত অসম্ভব, তাই নিজের জানার মধ্যে কত বিতর্কের অবকাশ আছে। (পাশাপাশি নতুন জ্ঞানের আলোয় তা পরিবর্তিত না হলে, তার থেকে তাঁরা সরেও আসেন না, আবার নতুনকে বিনা দ্বিধায় গ্রহণও করেন।)
তাই বিজ্ঞান আন্দোলন নিছক ধর্মবিরোধী আন্দোলন নয়। কিন্তু বিজ্ঞান তথা বস্তুবাদী দর্শন ধর্মবিরোধী অবশ্যই। বিজ্ঞানের সঙ্গে ভাববাদ, ঈশ্বরবিশ্বাস ও এই বিশ্বাসকেন্দ্ৰিক ধর্মের মিলনের নানা গন্তীর বাগাড়ম্বর ও সূক্ষ্ম প্রচেষ্টা, আসলে বিজ্ঞান আন্দোলনকে বিপথগামী করার এবং ভাববাদ ও ধর্মকে নতুন কৌশলে প্রতিষ্ঠা করার কৌশল মাত্র।
বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বরা (আসলে এরা সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী ব্যক্তিদেরই জ্ঞাতি ভাই) এবং তাদের অনুগত তথাকথিত শিক্ষিত ও এমনকি বিজ্ঞানের ডিগ্রিধারী ব্যক্তিরা নানা গুরুগম্ভীর লেখাপত্ৰ-আলোচনা-সেমিনারে এমনভাবে বিজ্ঞান ও ধর্মের মিলনের(২) কথা প্রচার করলেও, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, এ ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক বা অজ্ঞতাপ্রসূত কথাবার্তা আদতে শাসকশ্রেণীর স্বার্থবাহী এবং ধৰ্মজীবী পরজীবীদের আত্মরক্ষার উপায় মাত্র।
আসলে ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করার পথটি সঠিকভাবে আয়ত্ত করা দরকার। যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের অঙ্গ হিসেবে ধর্মের টিকে থাকা, সেই সমাজের পরিবর্তন ছাড়া ধর্মের অবস্থানেরও গুণগত কোন পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয়। ধর্ম সম্পর্কে বিজ্ঞান সম্মত তথ্য ও জ্ঞান অর্জন করার প্রক্রিয়াটি এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজ সম্পর্কে সচেতন হওয়ার প্রক্রিয়ার সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটিকে ছাড়া আরেকটি পরিপূর্ণতা পেতে পারে না। একইভাবে ধর্মের বিরদ্ধে সংগ্রামের বিষয়টি এই সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য যে সংগ্রাম, বা অন্তত শোষণ, আধিপত্য ও বৈষম্য দূর করার জন্য মানুষের যে লাগাতার দৈনন্দিন সংগ্রাম, তার সঙ্গে সম্পূক্তভাবে না। মিশলে সফল হতে পারে না। তা না করে, বিশেষত ধর্ম সম্পর্কে সচেতনতা না। বাড়িয়ে, বিচ্ছিন্নভাবে ধর্মের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলে মানুষের মধ্যে ধর্মকে আরো বেশি আঁকড়ে রাখার প্রবণতা সৃষ্টি হবে এবং ধর্মান্ধতা-সাম্প্রদায়িকতা-মৌলবাদ সৃষ্টি হওয়ার বা শক্তিশালী হয়ে ওঠার ব্যাপারটিই জোরদার হবে। ধর্ম তখন শহিদ হয়ে সহানুভূতি অর্জন করবে। ধর্ম যে নিপীড়িত মানুষকেই শহিদ করছে, এ বোধ জাগার আগেই ধর্মকে ও ধর্মবিশ্বাসীদের আঘাত করে গেলে ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তিগুলি মানুষকে বিভ্রান্ত করার সুযোগ আরো বেশী করে পাবে।
তাই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা বা মৌলবাদকে রুখতে গিয়ে, তখনো অসচেতন জনসাধারণের উপর শ্রেণীসচেতন বৈজ্ঞানিক হলেও ধর্মপরিচয়মুক্তি বা ধর্মবিরোধিতাকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা জনসাধারণকে এদেরই শক্ৰ করে তুলবে, আসলে যারা তার বন্ধুই হতে চাইছিল এবং মৌলবাদ ইত্যাদিকে তার বন্ধু করে তুলবে, আসলে যারা তার শত্রুই। ধর্ম ও তার এই ধরনের বিভিন্ন রূপ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করাটাই বড় দরকার, যে সচেতনতা অবশ্যই তার নিজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান বা সমস্যাবলী সম্পর্কে সচেতনতারই অংশ হিসেবেই হবে। এবং এই সচেতনতাই তাকে লড়াইয়ের সঠিক পথ খোঁজার উপযুক্ত করে তুলবে। এই লড়াই ধর্মের যে সব সামাজিক ভিত্তি, সেই অজ্ঞতা, অসহায়তা, বঞ্চনা, শোষণ, বৈষম্য ও দারিদ্র্য ইত্যাদি দূর করার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মেরও বিলুপ্তি ঘটাবে, কারণ তখন ঐভাবে ধর্মকে আঁকড়ে রাখার প্রয়োজন মানুষের আর থাকবে না। স্বাভাবিকভাবে তখন ধর্মকে কেন্দ্র করে অন্ধবিশ্বাস, সাম্প্রদায়িকতা বা মৌলবাদও শেকড়েই শুকিয়ে যাবে।
ব্যাপারটি এইভাবে বলে যাওয়া যেমন সহজ, বাস্তবে তার প্রয়োগ তেমনি অনেক জটিল, কঠিন ও দীর্ঘস্থায়ী প্রক্রিয়ার অংশ। নিয়তিবাদী বা স্বতস্ফুর্ততানির্ভর মানসিকতা থেকে যদি এমন ভাবা হয় যে ইতিহাসের নিয়মে ব্যাপারগুলি রয়ে সয়ে ঠিক ঘটে যাবে, তবে তা হবে আত্মঘাতী ও সুবিধাবাদী, পলায়নী একটি মনোবৃত্তির পরিচয়। একাজে অবশ্যই সচেতন বহুজনকে নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা নিতে এগিয়ে আসতে হয়, যে নেতৃত্ব কখনোই কর্তৃত্ববাদী, একনায়কতান্ত্রিক বা স্বৈরতান্ত্রিক হবে না।
মৌলবাদ একটি অসুস্থতা। ধর্ম তার বিপন্ন আস্তিত্বের সময় যেমন জঙ্গী মৌলবাদের মাধ্যমে তার ভিত্তিমূলকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তেমনি যারা এর নেতৃত্ব দেয় সেই গোষ্ঠী তার হতাশা ও সংকটের সময়, ক্ষমতা অর্জন করতে ধর্ম ও মৌলবাদকে কাজে লাগায়। শোষিত মানুষের যে অংশ তাদের সঙ্গী হয়। তারাও নিজেদের ক্রমবর্ধমান নানা সামাজিক সংকট, বিপন্নতাবোধ ও হতাশার ফলে প্ৰত্যারিত হয়।
মৌলবাদী অসুস্থতার সমাধানের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান দিক রয়েছে, (১) এর তাৎক্ষণিক চিকিৎসা, (২) এর স্থায়ী প্রতিরোধ। এই তাৎক্ষণিক চিকিৎসার ক্ষেত্রে চরম ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও কারো কারোর মাথায় আসে। যেমন আলজিয়ার্সে মুসলিম মৌলবাদীদের মৃত্যুদণ্ড। —
‘১৩ মৌলবাদীর মৃত্যুদণ্ড–তিউনিস, ৩০ মে-আলজিয়ার্সের এক বিশেষ আদালত ১৩ জন মৌলবাদী মুসলমানকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। ’৯২ সালে ঐ বিশেষ আদালত গঠন করা হয়। ইসলামি মৌলবাদের বিরুদ্ধে সরকারের লড়াইয়ের অঙ্গ হিসেবেই এই আদালত বসানো হয়। এ পর্যন্ত ৪৮০ জন মৌলবাদীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে এই আদালত। এ ছাড়াও ৫ জন জঙ্গিকে যাবজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে বিশেষ আদালত।–রয়টার’ (আনন্দবাজার পত্রিকা, ৩১.৫.৯৪)।
প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আলজেরিয়ার রাজধানী আলজিয়ার্স এবং আফ্রিকার এই দেশে জনসংখ্যার শতকরা ৯৯.১ জনই মুসলমান (সুন্নি) ও দেশটির রাষ্ট্ৰীয় ধর্ম ইসলাম। ইসলাম ধর্মাবলম্বীর এত সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি দেশে মুসলিম মৌলবাদীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ঘটনা এটি প্রমাণ করে যে, ইচ্ছা থাকলে মৌলবাদীদের শায়েস্তা করার কঠোরতম পন্থা অবলম্বন করা যায়ই। বাংলাদেশের যে মৌলবাদীরা তসলিমাকে হত্যার ফতোয়া দেয় কিংবা দরিদ্র অন্তঃসত্ত্বা এক রমনীকে নৈতিকতার দোহাই তুলে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ঢ়িল ছুড়ে মারার নির্দেশ দেয়, তাদের এই মৃত্যুদণ্ড দেওয়াটা মৌলবাদবিরোধিতার ঐকান্তিক ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশই হতে পারত। পাকিস্থান বা ইরানের মৌলবাদীদের কিংবা ভারতের হিন্দুত্ববাদীদের (আসলে যারা মৌলবাদী-ই) ঐ ধরনের অপরাধে কিংবা একটি জাতীয় ঐতিহাসিক সৌধ বিধ্বংস করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দিলেও ঐ ইচ্ছারই বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারত। আরব থেকে চীন নানা দেশেই ড্রাগপাচারকারীদের যেমন এইভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। মৌলবাদীদের ধর্মীয় ধান্দা এই ড্রাগব্যবসায়ীদের চেয়ে কোন অংশে কম বিপজ্জনক ও কম অপরাধমূলক নয়। বরং হয়তো বেশিই, কারণ ধর্মীয় মৌলবাদের মত ড্রাগ অন্তত বিপুল সংখ্যক ভিন্নধর্মের মানুষকে ঘূণা করতে ও নিশ্চিহ্ন করতে প্ররোচিত করে না। কাউকে হত্যা বা আত্মহত্যা করতে প্ররোচিত করা যদি অপরাধ হয়, তাহলে এইসব ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও মৌলবাদীরাও একই অপরাধে অপরাধী। তবে ড্রাগের বিরুদ্ধে লড়াই করা তুলনায় অনেক সহজ, কারণ ড্রাগ চোখে দেখা যায়। কিন্তু ধর্মাশ্রয়ী মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াই অনেক কঠিন, কারণ তার এই ধর্মীয় আশ্রয় চোখে দেখা যায় না বা ‘মিফার ডগ’ দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না। তা এক কায়াহীন মানসিক দিক, যা সরল ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে নানা স্তরে, নানা মাত্রায় মিশে থাকে।
তবে সাধারণভাবে আধুনিক বিশ্বে এই মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি একটি অমানবিক ও মনুষ্যত্ববিরোধী দিক। যত অপরাধে অপরাধীই হোক না কেন, ঐ অপরাধীরই মত একটি প্রাণকে নিশ্চিহ্ন করার অপরাধ করাকে সুস্থভাবে মেনে নেওয়া মুস্কিল। বিশেষত, কে প্রকৃত মৌলবাদী, সে কি অপরাধ করেছে, তাকে অপরাধী সাজানোর ক্ষেত্রে কোন রাজনৈতিক বা ভিন্নতর ষড়যন্ত্র আছে কিনা, মৌলবাদের সৃষ্টির পেছনে অমৌলবাদী হিসেবে চিহ্নিত ব্যক্তিদের ভূমিকাও শাস্তিযোগ্য কিনা, তার মৌলবাদী আচরণ সংশোধনের অতীত কিনা— ইত্যাদি নানা ব্যাপার এর সঙ্গে জড়িত এবং এ ব্যাপারটি বিতর্কিতও বটে। এ ব্যাপারে চরমভাবে সঠিক সিদ্ধান্তে আসাও দুরূহ।
তবু মৌলবাদীদের কঠোর আইনী শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত,-যাবজীবন কারাদণ্ড বা শ্রমশিবিরে পাঠানোর মত, যেমন দেওয়া হয়। হত্যাপরাধীদের। সতীদাহ, নদীতে শিশুনিক্ষেপ বা বহুবিবাহ প্রথার মত বর্বর ও তথাকথিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে আইন ও শাস্তি তাই বড় ভূমিকা পালন করেছে। একইভাবে ভিন্ন ধরমের মানুষের প্রতি বিষেদাগার করা, তাদের নিগৃহীত করতে অন্যদের প্ররোচিত করা, মানবিক মূল্যবোধগুলিকে অস্বীকার করা, ইত্যাদির মত যে সব আচরণ মৌলবাদীদের বৈশিষ্ট্য সেইগুলি প্রমাণিত হলেও আরো কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবং আন্তরিকভাবে তা প্রয়োগ করাও উচিত,–বর্তমানে যেমন ভারতবর্ষে ধর্ম ও জাতপাতকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক প্রচার কোন আইনী রাজনৈতিক দলের পক্ষে নিষিদ্ধ। (এ কারণে বিজেপি বা মুসলিম লীগ বহুৎ উসখুসি করলেও একটু সমঝে চলে, তবে তাদের হয়ে এ কাজ করে দেয় অন্য সমমনোভাবাপন্ন গোষ্ঠীগুলি।)
রাষ্ট্ৰীয় আইনী ব্যবস্থার পাশাপাশি মৌলবাদের চিকিৎসায় জনসাধারণের ব্যক্তিগত ও সাংগঠনিক প্রচেষ্টা আরো বেশি মূল্যবান। নিজেদের মানসিকতায় ধর্মান্ধতা, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদকে সচেতনভাবে পরিহার করার পাশাপাশি বিজ্ঞানমনস্কতা ও গণমুখী যুক্তিবাদ অনুসরণ করার অনুশীলন অতি গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভব ক্ষেত্রে যার মধ্যে এমন ধর্মান্ধতা ও মৌলবাদী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ দেখা যাবে, সক্রিয়ভাবে তার বিরোধিতাও করা উচিত। নিজের নিশ্চেষ্টতা প্রশ্রয়ের নামান্তর মাত্র। তবে এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার চেয়ে যৌথ সাংগঠনিক উদ্যোগই অধিকতত কার্যকরী। এলাকায় এলাকায় বিজ্ঞান ক্লাব থেকে শুরু করে ‘মৌলবাদ (বা সাম্প্রদায়িকতা) প্রতিরোধী সংস্থা’ জাতীয় অজস্র সংগঠন, প্রতিটি সচেতন ও শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তিদের গড়ে তোলা ও জনসাধারণের তৃণমূলস্তর আদি বিস্তৃত করা প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে তারা তা করেছেনও। কিন্তু প্রয়োজন আরো অনেক, অনেক বেশী।
এই ধরনের সংগঠন রাজনৈতিকও হতে পারে। ধর্মনিরপেক্ষ দক্ষিণপাহী এবং বামপন্থী আন্দোলনের ব্যাপকতা মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতায় বিষাক্ত পরিবেশকে কলুষমুক্ত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময়কার ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রাবল্যের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদের প্রসার এই ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলনের একটি মূল্যবান অংশ। (এ প্রসঙ্গে এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে, বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে ও যোগাযোগ ব্যবস্থার বিপুল প্রসারের সময়, কি অর্থনীতি, কি সংস্কৃতি ও সমাজনীতি কোনটিই বিশেষ দেশে গণ্ডিবদ্ধ থাকতে পারে না। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও লেনদেন ছাড়া কোন দেশে শুধুমাত্র সংকীর্ণ জাতীয়তা অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা ও বিশুদ্ধ নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি সম্ভব নয়।)
এবং মূল্যবান উপযুক্ত অর্থনৈতিক কর্মসূচীও। মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলি যে অর্থনৈতিক সংকটের সুযোগে তাদের গণভিত্তি গড়ে তোলার চেষ্টা করে, জনগণের ঐ সংকট ও দুরবস্থাকে দূর করার ক্ষেত্রে আন্তরিক ও বিকল্প উদ্যোগও জরুরী। এমন কি তা সংস্কারমূলক হলেও। তবে সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থবিমুক্ত, বৈষম্যহীন ও গণমুখী অর্থনৈতিক পরিকল্পনার জন্য এবং তাকে রূপায়িত করার জন্য আন্তরিকতটুকু অন্তত থাকা চাই। প্রকৃতপক্ষে মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলি অর্থনৈতিক সুখ-স্বপ্ন সহ যে সব মিথ্যা। আশা ভরসার কথা জনসাধারণের সামনে হাজির করে, তাদের প্রতিটিরই বাস্তব ও উপযুক্ত বিজ্ঞানসম্মত বিকল্প রাখা দরকার। এ ক্ষেত্রে মার্কসীয় দার্শনিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো একটি বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম, যদিও এর অর্থ এ নয় যে মার্কসবাদই শেষ কথা ও অদূরভবিষ্যতে আরো বিকশিত কোন প্রক্রিয়া মানুষ আয়ত্ত করবে না।
ধর্মীয় মৌলবাদ তথা ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতাকে যক্ষ্মারোগের সঙ্গে তুলনা করা যায়। অন্ধকারাচ্ছন্ন আলো-বাতাসহীন স্যাৎসেতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, উপযুক্ত পুষ্টি ও বিশ্রামের অভাব তথা প্রতিরোধ ক্ষমতার হ্রাস, তীব্র জীবাণু সংক্রমণ ইত্যাদি যক্ষ্মরোগ সৃষ্টির পথ সুগম করে। একইভাবে বিজ্ঞানমনস্কতার আলোর অভাব, অসচেতনতার অন্ধকার, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসহায়তার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ধর্মাশ্রয়ী ঐসব অসুস্থতাকে ডেকে আনে। ধর্মজীবী ধান্দাবাজেরা যক্ষ্মার জীবানুর মত মানুষের মনের এই অন্ধকারকে আশ্রয় করে তার জাল বিস্তার করে। অচিকিৎসিত যক্ষ্মারোগ তিলে তিলে শরীরকে ধ্বংস করে, উন্দরী থেকে মস্তিষ্কবিকৃতি জাতীয় নানা জটিলতার সৃষ্টি করে এবং এক সময় হঠাৎ করে মৃত্যুর দরজা খুলে যায়। অপ্রতিহত মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতাও মানুষ ও তার সমাজকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করতে থাকে, এক বিকৃত পিছিয়ে পড়া আদিমতার অন্ধকারের দিকে মানুষকে ঠেলে দেয়, ভ্রাতৃহত্যা থেকে উন্নয়নের স্থবিরত্ব জাতীয় নানা ধরনের জটিলতার সৃষ্টি করে এবং এক সময় ফ্যাসিস্টদের মত তার বিধ্বংসী প্ৰাবল্য নিয়ে জাতির উপর ঝাপিয়ে পড়ে। অচিকিৎসিত যক্ষ্মা শুধু ব্যক্তির মধ্যে সীমিত থাকে না, তা প্রবল সংক্রামকও বটে, নিকট মানুষদের মধ্যেও তার সংক্রমণ ঘটে, বিশেষত যাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম। অপ্রতিহত ধর্মান্ধতা-সাম্প্রদায়িকতামৌলবাদও শুধু কিছু ব্যক্তি বা একটি গোষ্ঠীতে সীমিত থাকে না, তা পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ায় অন্যদেরও উত্তেজিত করে তোলে এবং ভিন্ন ধর্মের অসচেতন ও মানসিক প্রতিরোধহীন ব্যক্তিদেরও স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে একই পন্থা অবলম্বন করে মোকাবিলার জন্য প্ররোচিত করে। যক্ষ্মার চিকিৎসায় জীবাণুকে মারার ওষুধের পাশাপাশি তার প্রতিরোধ অতি গুরুত্বপূর্ণ-উপযুক্ত পুষ্টি-বিশ্রাম-আলো-বাতাস ইত্যাদি রোগ নিরাময় ও প্রতিরোধের জন্য ওষুধের সঙ্গে অবশ্যই সুনিশ্চিত করা দরকার। মৌলবাদ জাতীয় অপশক্তির ক্ষেত্রেও তার চিকিৎসা ও প্রতিরোধের দিকগুলি একই সঙ্গে প্রযুক্ত হওয়া দরকার।
ধর্মীয় মৌলবাদ তথা ধর্মান্ধতা ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে গণমুখী যুক্তিবাদী চিন্তার প্রসার এবং বিজ্ঞানমনস্কতার আলোকোজ্জল পরিবেশ সৃষ্টি করা একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। অহংকার, অবিনয়, স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিকতার মত বদ্ধ পরিবেশ থেকে গণতান্ত্রিক বাতাবরণে মুক্তি এ ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শ্রেণীসচেতন অর্থনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জন করা এক বৈষম্যহীন ও পারস্পরিক সহযোগিতা নির্ভর সমাজব্যবস্থায় মৌলবাদের মত অপশক্তিগুলি তার টিকে থাকার বা সৃষ্টি হওয়ার জমিই হারায়।
ধর্মীয় মৌলবাদ প্রতিরোধে ধর্মপ্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচারও এ ব্যাপারে। সচেতনতাবৃদ্ধির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কিভাবে একসময় নিয়ানডার্থল আমলের মানুষ তার উন্নততর চিন্তা, অনুসন্ধিৎসা ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতার সাহায্যে একটি অতিপ্রাকৃতিক শক্তি ও মৃত্যুপরবর্তী প্রাণের কল্পনার জন্ম দিয়েছে, কিভাবে হাজার হাজার বছর ধরে এই কল্পনা ঈশ্বর আত্মা ও নানা ধর্মের সৃষ্টি করেছে, শ্রেণীবিভাজিত সমাজে কিভাবে শাসক ও শোষিত উভয়েই এই ধর্মকে ব্যবহার করেছে এবং কোন সামাজিক ও প্রাকৃতিক প্রতিকুল বৈরীশক্তির অস্তিত্বের কারণে এখনো বহু মানুষ এই ধর্মকে অনুসরণ করছে—এসবের অসূয়ামুক্ত ঔদ্ধত্যহীন বিনম্র বৈজ্ঞানিক আলোচনা ও প্রচার ব্যাপকভাবে করা দরকার। বিশেষত শ্রেণীবিভক্ত সমাজের এই গণবিরোধী সামাজিক শত্রুগুলিকে দূর করার উদ্যোগ ব্যাপকতর করার সঙ্গে মৌলবাদবিরোধিতার ও মৌলবাদপ্রতিরোধের প্রশ্নটি সম্পৃক্তভাবে যুক্ত।
এ কথাগুলি পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করেই এবং ধর্মের বিরুদ্ধে এ ধরনের পরোক্ষ লড়াই-এর পাশাপাশি প্রয়োজনে ধর্মের বিরুদ্ধে প্ৰত্যক্ষ সংগ্রাম চালানোরও সময় এসেছে,-বিশেষত ধর্মীয় মৌলবাদীদের সাম্প্রতিক ক্রমবর্ধমান দাপটের পরিবেশে। এর অর্থ কখনোই সরলধর্মবিশ্বাসী মানুষের অসহায় ধর্মবিশ্বাসকে অপমান ও ব্যঙ্গ করা নয়। কিন্তু অবশ্যই তার অর্থ বেদ-বাইবেল-কোরান-হাদিসমনুসংহিতাদির মত ধর্মগ্রন্থের বর্তমান অপ্রাসঙ্গিকতা, শ্রেণীভিত্তি, ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক দিকগুলিকে উন্মোচিত করা। পাশাপাশি তাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও প্রাচীন উপযোগিতাকে মর্যাদা দেওয়াও দরকার, দরকার তাদের উপর গোঁড়ামিমুক্ত গবেষণারও। ধর্মের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অর্থ খীশু-মহম্মদ বা যাজ্ঞবল্ক্যাদির প্রতি একপেশে, সবজান্তা ও উদ্ধত মানসিকতা থেকে অপমান ও ব্যঙ্গের বাণ নিক্ষেপ করা নয়। কিন্তু অবশ্যই তাদের মূল্যবান ঐতিহাসিক ভূমিকাকে উপযুক্ত মর্যাদা দিয়েই, এখনকার দিনেও তাদের হুবহু অনুসরণ করা ও অন্ধভাবে ভক্তিপ্রদর্শন করার মানসিকতাকে প্রতিহত করা। ধর্মের বিরুদ্ধে প্ৰত্যক্ষ সংগ্রামের অর্থ ধর্মীয় বাতাবরণে বিশ্বমানবিক সৌভ্রাতৃত্বের মত যে সব মানবিক মূল্যবোধের কথা যতটুকু বলা হয়েছে সেগুলিকে অস্বীকার করা নয়। কিন্তু অবশ্যই তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে এবং গ্রহণ-বর্জনের গোঁড়ামিমুক্ত মানসিকতা থেকে, ধর্মের তথা ঈশ্বর-নির্ভরতার নাম না করেই মনুষ্যত্ব ও মানবিক মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করা। (যেমন ‘বিশ্বমানবিক সৌভ্রাতৃত্ব’ বা ‘চুরি করা মহাপাপ’ জাতীয় কথাগুলি শুনতে ভাল লাগলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলি শাসকগোষ্ঠীর স্বাৰ্থবাহী। নিকট অতীতের বা বর্তমানের শ্রেণীবিভাজিত সমাজে পৃথিবীর সবাইকে ভাই বা বন্ধু ভাবার অর্থ শোষিত জনগণের কাছে শাসকশ্রেণীকেও সুহৃদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা অর্থাৎ অত্যাচারী শাসকের বিরুদ্ধেও শাসিতদের সংগ্রামকে দুর্বল করে দেওয়া। চুরি করা মহাপাপ’-এর প্রচারও আসলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সৃষ্টির পর, বৈষম্যভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায়, অর্থবানদের সম্পদরক্ষার একটি কৌশলমাত্র, যে সম্পদ তারা অর্জন করেছে নিজেদেরই নিয়ন্ত্রিত সমাজব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সুযোগ নিয়ে। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বমানবিক সৌভ্রাতৃত্বের’ মত কথাগুলি প্রকৃত মর্যাদা পাবে শ্রেণীহীন বৈষম্যমুক্ত সমাজে। এই সমাজে ‘চুরি করা মহাপাপ’-এর মত নীতিবাক্য প্রচারেরও কোন প্রয়োজন থাকবে না—এখনো যেমন আদিবাসী গোষ্ঠীর বহু মানুষ চুরির ব্যাপারটিই জানে না এবং এমন নীতিবাক্য তাদের কাছে হাস্যকর। চুরির বা পারস্পরিক বৈরিতার সৃষ্টিই হয়েছে শ্রেণীবিভাজনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তা যখন বিধ্বংসী ও শাসকশ্রেণীর পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়, তখন তারা নিজস্বার্থে নানা ধৰ্মকথার মাধ্যমে এমন নীতিবাক্যের সৃষ্টি ও প্রচার করে। যতদিন এই বিভাজন থাকবে, ততদিন এই ধরনের নীতিবাক্যের উপযোগিতাও থাকবে, কিন্তু তার পেছনের সত্যগুলিকে জেনে একটি বিজ্ঞানসম্মত মানবিক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়াই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। ধর্ম তথা ধর্মীয় নানা নীতিবাক্য-অনুশাসন-নির্দেশাদির প্রসঙ্গেও একথাগুলি প্রযোজ্য।)
প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় মৌলবাদী আটকাতে গিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে শুধু ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করা বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর একটি পদ্ধতি,–যা এক সময় ব্যর্থ হবে বাধ্য। কারণ প্রথমত, মানুষের সমস্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক দুরবস্থাগুলিকে টিকিয়ে রেখে এবং ধর্ম সম্পর্কে একটি স্তর আদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী অর্জন করার আগে, ধর্মকে শহিদ করলে ধর্ম তথা প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে আগ্রহ নতুন করে জেগে ওঠার সম্ভাবনাই বেশি। এবং এরই প্রতিক্রিয়ায় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তির এবং ধর্মান্ধতার পালে হাওয়াই লাগবে। ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই তার সামাজিক ভিত্তিগুলির বিরুদ্ধে লড়াইয়েরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। বস্তুবাদী দর্শনকে সামনে রেখে সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রেণীসচেতন সংগ্রামই ধর্মকে উচ্ছেদ করার সর্বোৎকৃষ্ট ও সবচেয়ে কার্যকরী পথ। বিচ্ছিন্নভাবে ধর্মকে দূর করা সম্ভব নয় অর্থাৎ সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক কোন ক্ষেত্রে সংগ্রাম পরিচালিত হওয়ার আগে বা না করে, শুধু ধর্মীয় মৌলবাদকে চূড়ান্তভাবে উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। এ কারণেই শ্রেণীসচেতনতাহীন বুর্জোয়া নাস্তিকতা কিংবা যান্ত্রিক যুক্তিবাদ কখনো ধারাবাহিকতা রক্ষা করে ব্যাপক মানুষকে ঈশ্বরবিশ্বাস থেকে প্রকৃত মুক্তি বা যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক মানসিকতা অর্জন করাতে পারে না। তাই চারপাশে এমন উদাহরণ কম নেই যে, সমাজে এ ধরনের নাস্তিক মানুষ যথেষ্ট আছেন, পাশাপাশি মৌলবাদও আছে শুধু নয়, নতুন করে সৃষ্টি হচ্ছে। অন্যান্য দেশের কথা ছেড়ে শুধু পশ্চিমবঙ্গের কথাই বলা যায়, যেখানে দীর্ঘদিনের বামপন্থী ও উদারপন্থী আন্দোলনের ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও কিংবা বুদ্ধিজীবীদের একাংশ যথেষ্ট উদার, ধর্মমোহমুক্ত বা নাস্তিক হওয়া সত্ত্বেও বিগত কয়েক বছরের মধ্যে ভারতীয় জনতাপাটি বা অখিল ভারতীয় বিদ্যাহী পরিষদের মত হিন্দুত্ববাদী ও ভিত্তিমূলে মৌলবাদী শক্তিগুলি তৃণমূলস্তর অব্দি তাদের প্রভাব, যতটুকুই হোক না কেন, বিস্তৃত করতে পেরেছে। একইভাবে এমন যুক্তিবাদী’রাও আছে যাদের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠা, আত্মপ্রচার ও নিজেকে সর্বোত্তম যুক্তিবাদী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগই বেশি; কুসংস্কারের শিকার সাধারণ মানুষদের তো বটেই, বিজ্ঞানমনস্কতার স্বপক্ষে আন্দোলনে রত অন্য ব্যক্তিদের হেয় করার প্রবণতাও রয়েছে। এবং যারা যান্ত্রিকভাবে কিছু ম্যাজিকপত্ৰ দেখিয়ে অলৌকিকতার বুজরুকি তুলে ধরাকেই প্রধানতম কাজ বলে মনে করেন। এই ধরনের ‘নাস্তিক’ বা যুক্তিবাদী’-দের কোন ইতিবাচক ভূমিকা নেই তা নয়, কিন্তু শেষ বিচারে ইতিবাচক কিনা তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ যথেষ্টই রয়েছে।
মার্কসীয় দর্শনকে সামনে রেখে (তা সে যত আলগাভাবেই ঝুলিয়ে রাখা হোক না কেন), ‘বামপন্থী’দের একটি বড় অংশ অন্যদিকে ধর্ম সম্পর্কে যে হাস্যকর অবস্থান গ্রহণ করেন তাতে পরোক্ষে ধর্মজীবীদের হাতই শক্ত হয়। মার্কসবাদ, বস্তুবাদী দর্শন ইত্যাদির কথা বলেও যখন দেখা যায়। এইসব বামপন্থীরা পাড়ার দুর্গাপূজা-কালীপূজার পৃষ্ঠপোষকতা করেন (যুক্তি?—জনসংযোগ), ঠনঠনিয়া বা দক্ষিণেশ্বরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় কপালে মাথা ঠোকেন (যুক্তি?-অভ্যাস), জ্যোতিষ আর কুষ্ঠিবিচার কিংবা শ্ৰাদ্ধ ও ধর্মীয় আচার মেনে বিয়ে করেন (যুক্তি?—জ্যোতিষে কিছু বিজ্ঞান আছে এবং শ্ৰাদ্ধ ইত্যাদি দেশীয় ঐতিহ্য) ইত্যাদি,-তখন অন্য মানুষদের কাছে ধর্মের (এবং ধর্মীয় মৌলবাদীদেরও) গ্রহণযোগ্যতাই বাড়ে। সাম্প্রতিক ভারতে বন্যার মত ছড়িয়ে পড়া ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদী দাপটের পেছনে স্থানীয় বামপন্থী আন্দোলনের (নিকট অতীতেও যার বৈজ্ঞানিক অবস্থান ছিল এবং এখনো সংখ্যালঘু কিছুজনের মধ্যে আছেই)। চরম বিচ্যুতি ও শূন্যতা বেশ কিছুটা ভূমিকা পালন করেছেই।
জনগণের আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্তভাবে মিশিয়ে বিজ্ঞানমনস্কতার স্বপক্ষে ও ধর্মপ্রসঙ্গে আন্দোলনও অবশ্যই করা দরকার। একটিকে ছাড়া আরেকটি সফল হতে পারে না। মাওসেতুং যেমন বলেছিলেন, ‘আমি যখন গ্রামাঞ্চলে ছিলাম তখন কৃষকদের মধ্যে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আমিও প্রচার চালিয়েছিলাম।’ এবং যেভাবে করেছেন তার একটি সামান্য পরিচয় কৃষকদের সামনে রাখা তাঁর বক্তব্য থেকে বোঝা যেতে পারে। —’ঐসব দেব ও দেবীরা বাস্তবিকই করুণার উদ্রেক করে। আপনারা শত শত বছর ধরে তাদের পুজো করে এসেছেন, অথচ তারা আপনাদের উপকারার্থে স্থানীয় উৎপীড়ক বা অসৎ ভদ্রলোকদের একজনকেও উচ্ছেদ করেনি। এখন আপনারা আপনাদের খাজনা কমাতে চান। আমি জিগ্যেস করতে চাই-কিভাবে আপনারা সেটা করবেন? আপনারা কি দেবদেবীর উপর বিশ্বাস করবেন, না কৃষক সমিতির উপর বিশ্বাস করবেন?’ (হুনানে কৃষক আন্দোলনের তদন্ত রিপোর্ট, মার্চ, ১৯২৭; নবজাতক প্রকাশন প্রকাশিত ‘মাওসেতুং-এর নির্বাচিত রচনাবলী’ থেকে)
আর এর ফলে গ্রামের ‘অশিক্ষিত কৃষকরাও কিভাবে ‘ধর্মীয় কর্তৃত্বের জোয়াল ছুড়ে ফেলতে পারেন, তার একটি পরিচয়ও তাঁর বর্ণনা থেকে পাওয়া যায়।–‘ভূস্বামীদের রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উচ্ছেদ ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই গোষ্ঠীগত কর্তৃত্ব, ধর্মীয় ও স্বামীর কর্তৃত্ব(৩) সবইটিলায়মান হয়ে পড়ে।. সর্বত্র যেখানেই কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠেছে, সেখানেই ধর্মীয় কর্তৃত্ব টলে উঠেছে। অনেক জায়গায় কৃষক সমিতি দেবদেবীর মন্দিরকে তাদের অফিসের কাজের জন্য দখল করে নিয়েছে। সর্বত্র তারা কৃষকদের স্কুল খুলবার কাজে বা সমিতির খরচ নির্বাহের জন্য মন্দিরের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে বলে। এটাকে তারা বলে ‘কুসংস্কার থেকে সাধারণের আয়’। লিলিং জেলায় কুসংস্কারমূলক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করা এবং মূর্তি ধ্বংস করার ধূম লেগেছে। এই জেলার উত্তরাঞ্চলীয় মহকুমাগুলোতে কৃষকরা মহামারীর দেবতাকে শাস্ত করার জন্য প্রজুলিত ধূপ-মোমবাতি নিয়ে শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। লুখীে-এর ফুপোলিংস্থিত তাও-মন্দিরে অনেক মূর্তি ছিল, কিন্তু কুওমিনতাংএর আঞ্চলিক সদর দপ্তরের জন্য যখন আরো ঘরের দরকার পড়ল, তখন ছোটবড় সব মূর্তিগুলোকে একসাথে কোণে গাদা করে রাখা হল। কৃষকরা এতে কোন আপত্তি তোলেনি। তারপর থেকে কোন পরিবারে কারো মৃত্যু হলে দেবদেবীর প্রতি উৎসর্গ, ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন এবং পবিত্র বাতি প্ৰদান করার ঘটনা খুবই কম ঘটেছে। …উত্তরের তৃতীয় মহকুমায় লোংফেং নানের কৃষকেরা এবং প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকেরা কাঠের মূর্তিগুলোকে কেটে সেই কাঠ দিয়ে মাংস রাঁধে। দক্ষিণের অঞ্চলে অবস্থিত তোংফু মন্দিরের তিরিশটিরও বেশি মূর্তিকে ছাত্র ও কৃষকরা মিলে পুড়িয়ে ফেলে।…’ ইত্যাদি। (ঐ) ধর্মীয় কর্তৃত্বের জোয়াল ভেঙ্গে বেরিয়ে আসা এমন মানুষদের কোন গোলাম আজম-বোল থ্যাকারে-খোমেইনিঋতম্ভরাদের দল তাদের শিবগরে পরিণত করবে?
এটি স্মর্তব্য যে মাওসেতুং এ রিপোর্ট দেন। চীনের মুক্তিরও ২২ বছর আগে, ১৯২৭-এর মার্চ মাসে। তারপর সারা চীন জুড়ে এমন কৃষক আন্দোলন সংগঠিত হয় তথা গণজাগরণ ঘটে কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে। আমেরিকায় ফান্ডামেন্টালিস্টরা, ভারতে হিন্দুত্ববাদী ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা, কিংবা মধ্যপ্রাচ্যে মুসলিম মৌলবাদীরা তাদের দাপট চালানোর সময় চীনের ঐ বিশাল ভূখণ্ডে এর ফলে এদের ছায়াও দেখা যায়নি।
সময় আরো এগিয়ে গেছে। শ্রেণীবৈষম্য ও সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন আরো বীভৎস ও সূক্ষ্মতর আকার ধারণ করেছে। এসবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বেড়ে উঠেছে ধৰ্মজীবীদের মৌলবাদী তাণ্ডব। কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩), ফ্রেডেরিখ এঙ্গেলস (১৮২০-১৯৮৫), এমনকি ভলাদিমির ইলিয়াভিচ লেনিন (১৮৭০-১৯২৪)-এর সময়েও ধর্মীয় মৌলবাদের সাম্প্রতিক ভয়াবহ রূপ সম্যক পরিস্ফুট হয়নি। এ অবস্থায় মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-এর ধর্মের বিরুদ্ধে প্ৰত্যক্ষ আন্দোলনের প্রাসঙ্গিক শিক্ষাকে নতুন করে ভাবা যায়। লেনিন লিখেছিলেন,–
‘মার্কসবাদ সবসময়ই সকল আধুনিক ধর্ম ও গীর্জা বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে, এবং প্রতিটি ধর্মীয় সংগঠনকে বুর্জোয়া প্রতিক্রিয়ার হাতিয়ার, যা শোষণের ব্যবস্থা রক্ষায় এবং শ্রমজীবী শ্রেণীকে হতবুদ্ধি করার কাজে ব্যবহৃত হয়, হিসেবে গণ্য করেছে।
‘একই সাথে এঙ্গেলস সেসব লোকেরও নিন্দা করেছেন, যারা সোস্যালডেমোক্রাটদের চেয়েও বেশি বামপন্থা’ বা ‘বেশি বিপ্লবী’ হতে চায়, যারা ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার লক্ষ্যে শ্রমিকের রাজনৈতিক দলের কর্মসূচীতে নাস্তিক্যবাদের সুস্পষ্ট ঘোষণা অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। লন্ডন প্রবাসী ব্লাংকুইপাষ্ট্ৰী কমিউনিষ্টদের বিখ্যাত ঘোষণাপত্র সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ১৮৭৪ সালে এঙ্গেলস ধর্মের ব্যাপারে তাদের উচ্চনাদের যুদ্ধ ঘোষণাকে নিবুদ্ধিতা হিসেবে অভিহিত করেন এবং বলেন যে, এ ধরনের যুদ্ধ ঘোষণা ধর্ম সম্পর্কে আগ্রহ নতুন করে জাগিয়ে তোলার এবং এটিকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার সর্বোত্তম পন্থা। এঙ্গেলস ব্লাংকুইদের দোষারোপ করে বলেন, তারা বুঝতে পারে না যে, একমাত্র শ্রমজীবী জনগণের শ্রেণীসংগ্রামই প্রলেতারিয়েতের ব্যাপক অংশকে সচেতন বিপ্লবী সামাজিক অনুশীলনের মধ্যে টেনে এনে নিপীড়িত জনগণকে ধর্মের জোয়াল থেকে প্রকৃতপক্ষে মুক্ত করতে পারে; আর এর বিপরীতে, ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে শ্রমিকদের রাজনৈতিক দলের একটি রাজনৈতিক কাজ হিসেবে ঘোষণা করা নেহাত-ই নৈরাজ্যবাদী বুলি কপচানো … এঙ্গেলস জোর দিয়ে বলেছেন যে, ধর্মের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক যুদ্ধ ঘোষণার জুয়াখেলায় জড়িয়ে না ফেলে প্রলেতারিয়েতকে সংগঠিত করা ও শিক্ষাদান করার কাজটি ধৈৰ্য্যের সাথে সম্পাদন করার সামর্থ্য শ্রমিকদের রাজনৈতিক দলের থাকা উচিত।
‘আমরা ধর্মের বিরুদ্ধে লড়ব-এটা সকল বস্তুবাদের এবং সবশেষে মার্কসবাদের গোঁড়ার কথা। তবে মার্কসবাদ এমন কোন বস্তুবাদ নয়, যা গোঁড়াতেই থেমে গেছে। মার্কসবাদ আরো এগিয়ে যায়। মার্কসবাদ বলে ৪ ধর্মের বিরুদ্ধে কিভাবে লড়তে হয়, তা আমাদের জানতে হবে এবং এ জন্যে আমরা জনগণের মধ্যে বস্তুবাদী পন্থায় বিশ্বাস ও ধর্মের উৎস ব্যাখ্যা করব। ধর্মকে মোকাবিলা করার ব্যাপারটি বিমূর্ত তত্ত্ব প্রচারের মধ্যে সীমিত রাখা যায় না এবং এ কাজটিকে এ ধরনের প্রচারে সীমাবদ্ধ করা যাবে না। এটিকে শ্রেণী আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট অনুশীলনের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে হবে, যার লক্ষ্য ধর্মের সামাজিক মূলগুলোকে নির্মূল করা।’ (লেনিন, সংগৃহীত রচনাবলী, খণ্ড ১৬, ইংরেজি সংস্করণ, প্রোগ্রেস পাবলিশার্স, মস্কো, ১৯৭৩, পৃঃ ৪০৩, ৪০৪ ও ৪০৫, গুরুত্ব আরোপ লেনিনের। এখানে অনীক, মে, ১৯৯৫-এ প্রকাশিত সাদেক রশিদ-এর ‘প্ৰসঙ্গ ৪ তসলিমা নাসরিন’ থেকে সংগৃহীত, অনুবাদ তীরই।)
ধর্মের বিরুদ্ধে (এবং এইভাবে ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে) কিভাবে লড়তে হবে অবশ্যই তা আমাদের জানা দরকার। এক্ষেত্রে কোন সন্দেহ নেই যে, এই লড়াই করতে হবে জনসাধারণের মধ্যে থেকে, তাদের দৈনন্দিন অর্থনৈতিক সংগ্রামের সাথী হয়ে। চীনের পূর্বোক্ত অভিজ্ঞতা যেমন এটিও জানায় যে, আসলে ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী শোষিত মানুষই, যাঁরাই মূলত ধর্ম ও ধর্মীয় মৌলবাদের দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। এবং তাঁরা তা করবেন তাদের সামগ্রিক আন্দোলনের অংশ হিসেবেই। সচেতন ব্যক্তিদের দায়িত্ব হচ্ছে তাদের সংগঠিত করে সঠিক দিশার সঙ্গে পরিচিত করা এবং তাঁদেরই হাতে নেতৃত্ব ছেড়ে দেওয়া। বর্তমান বিশ্বে এই ‘শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী’ মানুষের সঙ্গে বিপুল সংখ্যক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছে, যাদের মধ্যে রয়েছে উচ্চ মাইনের তথাকথিত শ্রমিক থেকে নানা স্তরের বুদ্ধিজীবীরাও। এদের মধ্যে সচেতনতা ও বিজ্ঞানমনস্কতার আন্দোলন যেমন গড়ে ওঠে, তেমনি, ধর্মসহ প্রতিষ্ঠানিক বিভিন্ন কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে তাদের কারো কারোর স্বাৰ্থও গাঁটছড়া বাধা। তবু এই স্তরের ব্যক্তিদের একটি বড় অংশই ধর্মের বিরুদ্ধে তথা ধর্মীয় মৌলবাদের মত নানা অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াইতে সামিল হবেন। এবং ধর্মীয় মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধিতার বিরুদ্ধে লড়াইতে সাধারণ ধর্মবিশ্বাসীরাও অংশগ্রহণ করতে সক্ষম। ধর্মবিশ্বাসী মাত্রেই মৌলবাদী নন এবং তাঁদের অনেকেই মৌলবাদকে ঘূণাও করেন (যদিও ধর্ম তাদের অনেকের নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসের মত)। মৌলবাদের বিরুদ্ধে লড়াইতে এই ধরনের বিভিন্ন স্তরের মানুষই শরিক।
এঙ্গেলস যখন ধর্মের ব্যাপারে ‘উচ্চনাদের যুদ্ধ ঘোষণাকে নিবুদ্ধিতা হিসেবে অভিহিত করেন।’ তখন সাম্প্রতিক কালের হিন্দু-মুসলিম-খৃস্ট মৌলবাদীরা দূরের কথা, আমেরিকায় ফান্ডামেন্টালিস্টরাই সুসংগঠিত হয়ে ওঠেনি। একইভাবে মার্কসএঙ্গেলস-এর সময়ে ফ্যাসিবাদেরও উদ্ভব ঘটেনি, দেশে দেশে নয়া ফ্যাসিস্ট ধর্মীয় মৌলবাদের ক্রমবর্ধমান তাণ্ডবও দেখা যায়নি। তাই ধর্ম প্রসঙ্গে লড়াইয়ের জায়গাটা এখন শুধু ধর্মে আবদ্ধ নেই, তা একটি বিশেষ মাত্রা পেয়ে আরো হিংস্র, উগ্র, গোঁড়া ও অন্ধ মৌলবাদীদের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছে। এক্ষেত্রে নিজেদের নিছক ধর্মীয় কর্তৃত্বের জোয়াল থেমে মুক্ত করার দীর্ঘস্থায়ী ধৈর্যসাপেক্ষ প্রক্রিয়া নয়, মৌলবাদের বিরুদ্ধে দ্রুতগতির লড়াইও চালানো দরকার। কোন এক দূর বা অদূর ভবিষ্যতে ‘ধর্মের সামাজিক মূলগুলোকে নির্মূল করার’ মধ্য দিয়ে ধর্মের স্বাভাবিক বিলুপ্তি ঘটবে,-স্পষ্টতঃ তখন ধর্মীয় মৌলবাদের অস্তিত্বেরও কোন প্রশ্ন আসে না। কিন্তু এখনকার জঙ্গী মৌলবাদীদের রুখতে, বিশেষত ‘শ্রেণীসংগ্রামের’ বর্তমান বিভ্রান্তিকর পরিবেশে, মৌলবাদ প্রসঙ্গে বিশেষ কর্মসূচী নেওয়া দরকার। শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর করা, সমমনস্ক ব্যক্তিদের সংগঠিত করা, শোষিত জনগণকে সংঘবদ্ধ করে। শিক্ষাদান করার কাজ আরো বিকশিত হওয়া যেমন উচিত, তেমনি প্ৰত্যক্ষভাবে শুধু ধর্মের প্রসঙ্গে প্রচার অ্যাগের চেয়ে, (অন্তত মার্কস-এঙ্গেলস-এর আমলের চেয়ে) অনেক বেশি গুরুত্ব পাওয়া দরকার।
‘শ্রমিকদের রাজনৈতিক দলের কর্মসূচীতে নাস্তিক্যবাদের সুস্পষ্ট ঘোষণা অন্তর্ভুক্ত’ করার মত পরিস্থিতি এখনো হয়তো আসেনি, কিন্তু ধর্ম প্রসঙ্গে বিজ্ঞানমনস্কতার ও মৌলবাদ-বিরোধিতার সুস্পষ্ট ঘোষণা অন্তর্ভুক্ত করার সময় এসেছে এবং গণবিজ্ঞান আন্দোলনের পাশাপাশি শ্রেণী সচেতন ও বস্তুবাদী দর্শনে শিক্ষিত নাস্তিক্যবাদী সংস্থার প্রয়োজনও এখন অনেক বেশি বলেই প্রতীয়মান হয়। এটি ঠিক যে, এখন থেকে ৭০ বছরেরও বেশি সময় আগে চীনের হুনানে সঠিক পথে সঠিক নেতৃত্বে পরিচালিত অল্প কয়েক বছরের কৃষক আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে কৃষকরা যেমন ধর্মীয় কর্তৃত্বের জোয়াল ভেঙে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে প্রস্তুত হয়েছিলেন, বর্তমান বাংলায়, ভারতে বা অন্যান্য কিছু দেশে দীর্ঘ কয়েক দশকের ‘বামপন্থী কৃষক আন্দোলনের’ পরে অন্তত ধর্মীয় ক্ষেত্রে ঐ প্রস্তুতির অনেকটাই এখনো বাকি। কবে এই আন্দোলন ‘বামপন্থী’ হবে ও রাজনৈতিক মৌলবাদী মানসিকতামুক্ত হবে কে জানে! তবু অন্তত ধর্মীয় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধিতার প্রশ্নে এই ধরনের সমস্ত বামপন্থী সংগঠনের মধ্যকার ঐক্য এবং ধর্মনিরপেক্ষ ও নাস্তিক্যবাদী সংস্থা বা গণবিজ্ঞান সংগঠনগুলির সঙ্গে সহযোগিতামূলক কর্মসূচী যে নেওয়া হবে —এ আশা ব্যক্তি করা যায়।
এঙ্গেলস ভয় করেছিলেন, ধর্মের বিরুদ্ধে উচ্চনাদের যুদ্ধ ঘোষণা ধর্মের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়িয়ে তুলবে এবং ধর্মকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করবে। এখনকার পরিস্থিতিতে এটিও কতটা সত্য তা ভেবে দেখার সময় এসেছে। এর বড় কারণ ধর্মের বিরুদ্ধে উচ্চনাদের যুদ্ধ ঘোষণা এখন কোন রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে প্রাথমিকভাবে ততটা আসছে না, যতটা আসছে মূলত মানুষের দ্রুত বিকশিত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের তথা প্রকৃতি সম্পর্কে সত্য উপলব্ধির থেকে। বিবর্তনবাদ ছিল এ ধরনের প্রথম বড় যুদ্ধ ঘোষণা। তারপর জৈব অণুর কৃত্রিম সৃষ্টি থেকে কোয়ান্টামতত্ত্ব বা আপেক্ষিকতার তত্ত্ব সহ ব্ৰহ্মাণ্ড সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান জ্ঞানের এই পরিবেশে ঈশ্বর ও ঈশ্বর বিশ্বাসকেন্দ্ৰিক ধর্মের অবস্থানটিই ক্ৰমশঃ হাস্যকর হয়ে উঠছে। এ অবস্থায় স্বাভাবিকভাবে ঐ অনুযায়ী ঐতিহ্যমণ্ডিত মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীও পরিবর্তিত হচ্ছে। কেঁপে উঠছে ধর্মের ভিত্তি। এর প্রতিক্রিয়ায়ও ধর্মান্ধতা বা মৌলবাদের সৃষ্টি হয় ও হচ্ছে, কিন্তু তা আটকাতে এই উচ্চনাদের যুদ্ধ ঘোষণা তথা জ্ঞানচর্চা বন্ধ হবে না, হওয়া উচিতও নয়। অর্থনৈতিক-ও শ্রেণী-সংগ্রামের পাশাপাশি এই বৈজ্ঞানিক সত্যোপলব্ধিও ধর্ম তথা ধর্মীয় মৌলবাদের মৃত্যুঘণ্টা বাজাবে।
এখন থেকে ১০০ বছর আগে, এঙ্গেলসদের সময় ধর্মের বিরুদ্ধে তীব্র লড়াইয়ের ডাক ধৰ্মকে শহিদ করে তার প্রতি মানুষের সহানুভূতি বাড়াত। কিন্তু এখন হুবহু এ পরিস্থিতি নেই, যদিও এ ধরনের সহানুভূতি পাওয়ার পরিবেশ স্থানবিশেষে একেবারে নেই তা-ও নয়। তবে এখন পৃথিবীর ১১৫ কোটিরও বেশি মানুষ ধর্ম ও ঈশ্বরের মোহ থেকে মুক্ত, কয়েক দশক আগেও যা ভাবাই যেত না। এঁদের মধ্যে উদার বুর্জেয়া, অজ্ঞাবাদী (agnostic) ও বিজ্ঞানীসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ যেমন আছেন, তেমনি আছেন মার্কস-এঙ্গেলসদেরই শিক্ষায় উদ্ধৃদ্ধ মানুষও। এছাড়া আরো বহুসংখ্যক মানুষই রয়েছেন যাঁরা অতি আলগা ভাবেই (কখনো বা নিছকই সুবিধাজনক হিসেবে) ধর্মও ঈশ্বরকে আঁকড়ে আছেন এবং এঁদের বৃহদংশ দোদুল্যমান অবস্থায় থাকেন। প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক ও ধর্মপরিচয়মুক্ত হিসেবে নিজেদের সরকারীভাবে ঘোষণা না করা বাকী প্রায় শতকরা ৭৯-৮০ ভাগ পৃথিবীবাসীরও ৯০ ভাগই প্রকৃত বা আদৌ ধর্মাচরণ করেন না বলেই জানা গেছে। এঁদের কাছে ধর্মপরিচয় ও ঈশ্বর একটা কায়াহীন ঐতিহ্যগত অভ্যাস মাত্র। এছাড়া কয়েক শতাব্দী পূর্বে তো বটেই, বিগত শতাব্দীতেই ধর্ম যেমন রাষ্ট্ৰীয় ক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা পালন করত, এখন ঐ পরিস্থিতিও নেই।
সব মিলিয়ে, ১৮৭৪ সালে এঙ্গেলস ধর্মের বিরুদ্ধে উচ্চনাদের যুদ্ধ ঘোষণাকে ধর্ম সম্পর্কে আগ্রহ নতুন করে আগ্রহ জাগিয়ে তোলার এবং এটিকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষণ করার সর্বোত্তম উপায় হিসেবে যে অভিহিত করেছিলেন, এই ১২০ বছর পরে ঐ পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়েছে কিনা, তা ভেবে দেখার সময় বামপন্থীদেরও এসেছে, বিশেষত মৌলবাদীদের সাম্প্রতিক দাপটের পরিস্থিতিতে এবং আন্তর্জাতিক ভাবে বামপন্থী আন্দোলনের বিভ্রান্তির সময়ে। শ্রেণী সংগ্রাম ও শোষিত মানুষের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী প্রচারের গুরুত্বকে সামান্যতম খাটো না করেও এটি বোধহয় বলা যায় যে, ধর্মের বিরুদ্ধে উচ্চনাদের যুদ্ধ ঘোষণার পরিস্থিতি ও সময় এগিয়ে এসেছে। বাস্তবিক দেখা যাচ্ছে, ধর্মের বিরুদ্ধে এ ধরনের লড়াইয়ের ডাক দেওয়ার ফলে মৌলবাদীরা যেমন ক্ষিপ্ত হচ্ছে, তেমনি পৃথিবীর বহু মানুষ এই লড়াইকে সমর্থন করতেও এগিয়ে আসছেন। এরা নানা ধরনের উদ্দেশ্য থেকে তা করতে পারেন, কিন্তু মৌলবাদ প্রতিরোধে এদের এই ভূমিকা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের লড়াইয়ের প্রতিক্রিয়ায় মৌলবাদীরা যে হিংস্ৰ মনোভাব প্রকাশ করে, তাতে তাদের স্বরূপ আরো নগ্নভাবে মানুষের সামনে পরিস্ফুটও হয়। (সম্প্রতি তসলিমা নাসরিন বা সলমন রুশদির মত ব্যক্তিদের সমর্থনে নানা স্তরের মানুষ যেভাবে সমবেত হয়েছেন, তাতে এটি স্পষ্ট যে, ধর্মের বিরুদ্ধে তীব্র ও প্রত্যক্ষ লড়াই ধর্মকে ‘মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার সর্বোত্তম পন্থা’ আর নয়। পুঁজিবাদী সংস্কৃতির ধারক ও বাহকেরা নিজ স্বার্থে ও আপন অস্তিত্বের স্বার্থে এঁদের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে এগিয়ে আসছে, এটি হয়তো আংশিক সত্য এবং এ ব্যাপারে বিতর্কের অবকাশও আছে। কিন্তু সাম্প্রতিক দুনিয়ায় মৌলবাদ প্রতিরোধে যে মৌলবাদ-বিরোধী ব্যাপক যুক্তফ্রন্ট গড়ে তোলা দরকার তাতে এ ধরনের ব্যক্তি ও তাদের সমর্থকদের ভূমিকা অবশ্যই মূল্যবান ও অবিচ্ছেদ্য)।
মৌলবাদের স্থায়ী প্রতিরোধে শ্রেণীসংগ্রাম ও দীর্ঘস্থায়ী প্রচার অবশ্যই থাকা প্রয়োজন। তা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের অংশও বটে। কিন্তু মৌলবাদ যখন দরজায় কড়া নাড়ছে, তখন কবে জনগণ সংগঠিত হয়ে একটি সঠিক, বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন বা শ্রেণীসংগ্রাম শুরু করবেন, ঐ অপেক্ষায় দরজা বন্ধ করে বসে না থেকে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ের উদ্যোগও গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত ধর্ম যখন বিশেষ শ্রেণীর একটি শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হয়ে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার জন্ম দিচ্ছে, তখন ধর্মের এই ব্যবহারের বিরুদ্ধে এবং মৌলবাদসাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে প্ৰত্যক্ষ সংগ্রাম করার অর্থ ‘শ্রেণীসংগ্ৰাম’-ই করা,–তা আংশিক হলেও এবং তাকে এইভাবে চিহ্নিত না করা হলেও। মৌলবাদের তাংক্ষণিক চিকিৎসার জন্য এই লড়াইয়েরই অংশ ধর্মের বিরুদ্ধে উচ্চনাদের যুদ্ধ ঘোষণাও।
মৌলবাদ বিরোধী জনগণের ব্যাপক যুক্তফ্রন্ট এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দেবেন। এই যুক্তফ্রন্টে বামপন্থী বিপ্লবী থেকে সরল ধর্মবিশ্বাসী ব্যক্তিরা যেমন, তেমনি মৌলবাদবিরোধী বুর্জেয়া ব্যক্তিত্ব থেকে বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী মানুষরাও যুক্ত হবেন। ফ্যাসিবাদ প্রতিরোধে বা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে যেমন ব্যাপক যুক্তফ্রন্টের প্রয়োজন, তেমনি ফ্রন্টের প্রয়োজন ধর্মীয় মৌলবাদ প্রতিরোধের ক্ষেত্রেও। ধর্মীয় মৌলবাদ সম্পূর্ণত (অন্তত বাহ্যিকভাবে) ধর্মকেন্দ্ৰিক ধর্মের রীতিনীতি, অনুশাসন, আচার অনুষ্ঠানকে সামনে রেখেই তার জন্ম ও বেঁচে থাকা।
হতে পারে না। এর ফলে ধর্ম সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে কিনা তা অন্য প্রশ্ন, কারণ এটি জড়িত প্ৰাকৃতিক ও বিশেষত সামাজিক জনবিরোধী প্রতিকুল শক্তিগুলির সম্পূর্ণ উচ্ছেদের সঙ্গে। কিন্তু মৌলবাদকে আটকাতে,-’এখনকার জাতীয় ও আন্তজার্তিক পরিস্থিতিতে, ‘শ্রেণী:আন্দোলনের সুনির্দিষ্ট অনুশীলনের’ লক্ষ্য সামনে রেখেও তার জন্য শুধু অপেক্ষা করে গেলে, বড় বেশি দেরি হয়ে যাবে না তো?
***
হ্যাঁ, দেরি হয়েই যাচ্ছে।
সাম্প্রতিককালে ভারতীয় ভূখণ্ডে হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি ও মৌলবাদীদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব যেমন এর অন্যতম দিক, তেমনি আফগানিস্থানে তালিবানদের উদ্বেগজনক উত্থান তার আরেকটি উল্লেখযোগ্য নির্দেশক।
ভারতের হিন্দু মৌলবাদীদের জোট নানা কৌশলে জনসাধারণের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা ও ভিত্তি বিস্তুত করে চলেছে। এরা তাদের মূল লক্ষ্য অর্থাৎ রাষ্ট্ৰক্ষমতা দখলের ও হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনাকে অপরিবর্তিত রেখে, এই লক্ষ্য অর্জনের কৌশলগুলি সুবিধাজনকভাবে পাল্টায়। কখনো তারা অযোধ্যায় রামমন্দির গড়া ও বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার আহ্বান জানায়, কখনো বা প্রতিশ্রুতি দেয় দুনীতিমুক্ত প্রশাসন ও উন্নত স্বনির্ভর অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার। দোহাই দেয় নিজস্ব সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, তথাকথিত জাতীয়তা ইত্যাদি নানাবিধ মনোমুগ্ধকর ও বিভ্রাস্তিকর বিষয়ের।
হিন্দু মৌলবাদীদের অন্যতম মুখপত্ৰ স্বামী মুক্তানন্দ স্পষ্টই বলেছিলেন, ‘হিন্দুর নামে যে রাজনীতি করে তাকেই আমরা শ্রেষ্ঠ বলে মানি। কারণ হিন্দুরা সাম্প্রদায়িক নয়।’ এবং ১৯৯২-এর ৬ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভাঙ্গা প্রসঙ্গে তার বক্তব্য, ‘ওগুলির ধ্বংস কেবলমাত্র হিন্দুমন্দির ধ্বংসের প্রতিশোধেই ঘটে। হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে কখনোই মসজিদ ধ্বংস করে না। কিছু বালক যেমন ফুর্তি করার জন্য মসজিদ ভাঙ্গে’ (মেইনষ্ট্ৰীম, ৩০.১০.৯৩)।
হিন্দু মৌলবাদীদের প্রধান রাজনৈতিক সংগঠন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) তার ১৯৯৬-এর নির্বাচনী ইস্তেহারে দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করে ‘হিন্দুত্বই সেই একমাত্র সংযোগসূত্র যা আমাদের জাতির ঐক্য এবং সংহতি রক্ষা করতে পারে।’–হ্যাঁ, এদের কাছে ভারতীয় হিসেবে পরিচয় নয়, হিন্দু হিসেবে পরিচয়ই একমাত্র গ্রহণীয়। তাই ১৯৮০ সালে প্রথম বিশ্বহিন্দু পরিষদের প্রকাশ্য ঘোষণা—All nonHindus are aliens (সমস্ত অহিন্দুই বিদেশী)
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আমেরিকা বা প্রথম বিশ্বের দেশগুলির প্রতি এদের দুর্বলতা, তথা সাম্রাজ্যবাদী ও কম্যুনিজম-বিরোধী শক্তিগুলির সঙ্গে এদের সহমর্মিতার আঁচও নানা ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। বিজেপির নির্বাচনী ইস্তেহারে যেমন বলা হয়েছে ‘চীন যে পাকিস্থানকে অস্ত্র ও নানাবিধ সাহায্য করছে সে সম্পর্কে উদাসীন হলে চলবে না।’ অথচ একই ধরনের কাজ আমেরিকা ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী দেশ ও বহুজাতিক সংস্থারা করলেও সে সম্পর্কে তা নীরব।
শিক্ষা, নারী, অর্থনীতি, বৈদেশিক নীতি-ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে হিন্দুত্বকেন্দ্ৰিক ভয়াবহ মৌলবাদী ভাবনাকে নানা কৌশলে ভারতীয় জনমাসনে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছে। এরইসঙ্গে নানা ধরনের রাজনৈতিক সুবিধাবাদ, ধান্দাবাজি ও বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে হয়তো কয়েক বছরের মধ্যে ভারত একটি হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত হয়ে যাবে,-যখন ‘ভারত’ বা ‘ইন্ডিয়া’ নামটি মুছে দিয়ে রাষ্ট্রের নাম হবে হিন্দুস্থান, যে রাষ্ট্রে ধর্মপরিচয়ই হবে নাগরিকদের প্রধানতম পরিচয়, তথাকথিত হিন্দুনেতারা ও তাদের মধ্যেও মূলত উচ্চবর্ণের হিন্দুরাই থাকবে শাসন ক্ষমতায়, এই শাসকগোষ্ঠীরও নৈতিক নেতৃত্ব দেবে পরিশ্রমজীবী সাধুসন্তের দল, হিন্দু ছাড়া ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা হবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক, সম্প্রদায়গত দাঙ্গা ও অসহিষ্ণুতা হবে তীব্র, নারীরা হবে গৃহকোণে আবদ্ধ ও শুধুমাত্র সস্তানের জন্মদাত্রী, সমস্ত ধরনের মুক্ত উদার ও বৈজ্ঞানিক চিন্তা হবে কঠোরভাবে অবদমিত, সাম্রাজ্যবাদী শোষণ হবে আরো তীব্র ও সূক্ষ্ম, শিক্ষাদীক্ষা হবে মধ্যযুগীয় ইত্যাদি। হিটলারের ইহুদি নিধনের মত মুসলিম-খৃষ্টানদের গণহত্যাও ভিন্ন পদ্ধতিতে সংঘটিত হতে পারে,-যদি না তারা নিঃশর্তে হিন্দুত্বকে বরণ করে।
এই হিন্দু-মৌলবাদী ফ্যাসিবাদী অপশক্তিকে প্রতিহত করার ক্ষেত্রে মানবপ্রেমিক-দেশপ্রেমিক ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁদের এই ঐক্য এখনো আশানুরূপ পর্যায়ে পৌঁছয় নি। মৌলবাদের উত্থান প্রতিরোধে বামপন্থী সহ প্রতিষ্ঠিত তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলির আন্তরিকতার অভাবও অনুভব করা যায়-যার প্রতিফলন ঘটছে বিভিন্ন রাজ্যে, এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও, পঞ্চায়েত-পুরসভাসহ নানা ক্ষেত্রের নির্বাচনে কিছু কিছু আসনে হিন্দুত্ববাদীদের বিজয়ী হওয়ার মধ্যে। এরই মধ্যে আবার কোন কোন ‘লড়াকু’। নেতা বা নেত্রী তার প্রধান শত্রু হিসেবে ‘বামপন্থীদের’ চিহ্নিত করছেন এবং হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলির সম্পর্কে একেবারেই নীরব। ব্যাপারটি উভয়ের গোপন আঁতাত ও সহমর্মিতার ইঙ্গিত দিতে যথেষ্ট এবং অদূর ভবিষ্যতে তা তাঁদের ক্ষমতায়ও বসাতে পারে–যদি না শুভবুদ্ধির উদয় হয় ও সুদৃঢ় প্রতিরোধ আসে।
তাই দেরি হয়েই যাচ্ছে।
অন্যদিকে পৃথিবীর নানা কোণে খৃষ্টীয় মৌলবাদীরাও বসে নেই। কিন্তু আন্তর্জাতিকভাবে বড় বেশি বিলম্বিত হচ্ছে ইসলামী মৌলব্লাদীদের প্রতিহত করার কাজটিও। ইরানের মত কিছু ক্ষেত্রে সাময়িকভাবে হলেও অবস্থার কিছু পরিবর্তন তবু একটু আশা জাগায়। ইরানে সম্প্রতি (অগাস্ট, ১৯৯৭) নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে মহম্মদ খাটামি শপথ নিয়েছেন। ইনি ধর্মপ্ৰাণ হলেও আগের কট্টরপন্থীদের তুলনায় উদার। শপথ নেওয়ার অব্যবহিত পরে একজন নারীকে ভাইসপ্রেসিডেনটের পদ দিয়েছেন—১৯৭৯-এর ‘ইসলামী বিপ্লবের’ পর এই প্রথম। ইরানের কঠোর ইসলামী বিধিকে সরলীকরণ করা ও দুর্বল অর্থনীতিকে চাঙ্গা কবার জন্যও খাটামির প্রতিশ্রুতি আশাব্যঞ্জক। তবু কট্টরপন্থী ইসলামী মৌলবাদীরা তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালু রেখেছে এবং শেষ অব্দি তিনি কতটা সফল হবেন তা এখনি বলা মুস্কিল।
কিন্তু এরই পাশাপাশি আফগানিস্থানে তালিবানদের উত্থান উদ্বেগজনক৷ ১৯৯৬-এর ২৭শে সেপ্টেম্বর তালিবানরা আফগানিস্থানে প্রেসিডেন্ট রব্বানিকে ক্ষমতাচুত করে কাবুল দখল করে। ক্রমশ বহির্বিশ্বের মানুষ জানতে পারে মৌলবাদীরা ক্ষমতায় এলে কিভাবে মানুষের অগ্রগতির ইতিহাসকে পেছনে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। মধ্যযুগীয় শরীয়তি ইসলামী আইন, মেয়েদের উপর নানা ধরনের ফতোয় ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তালিবানরা তাদের ফ্যাসিবাদী চরিত্রের প্রকাশ ঘটায়।
আরবীতে ‘তালিব’ কথার অর্থ ছাত্র; বহুবচনে তালিবা (Taliban)। শুরুতে ছাত্রদের হাতেই গঠিত হয়েছিল এই বিপ্লবী ইসলামী বাহিনী। তালিবান সরকারের একটি ইতিবাচক দিক হল, কঠোর আইন প্রয়োগে দুনীতিগ্রস্ত আমলা ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের শায়েস্তা করা। কিন্তু ব্যাপারটি. এই নয় যে, এই ধরনের কঠোর শরীয়তি আইন না থাকলে এদের শাস্তি দেওয়া যেত না। অন্নসলে পূর্বতন সরকারেরও দুনীতি দমনের আইন ছিল। কিন্তু তার উপযুক্ত প্রয়োগ ঘটত না এবং ছিল ‘সর্ষের মধ্যেই ভূত। সাম্প্রতিক ভারতে যেমন লালু-জয়ললিতা-রাও-ভগত প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা ও তাদের পরবর্তী স্তরের বহু নেতা ও আমলারা জনসাধারণের অর্থ আত্মসাৎ, স্বজনপোষণ, খুন, প্রতারণা, সীমাহীন বিলাসব্যসন ইত্যাদি নানা অপরাধে অভিযুক্ত হলেও, তাদের বিচার কবে শেষ হবে এবং অপরাধী হলে, কবে তারা শাস্তি পাবে—এ ব্যাপারটিই এখনো বিশ বঁও জলে। আফগানিস্তানেও বিগত কয়েক বছরে দুনীতির ছবিটা ছিল একইরকম। তালিবানরা এ ছবিকে নিঃসন্দেহে কিছুটা পাল্টেছে। ব্যাপারটি কঠোর শরীয়তি আইনের প্রয়োজনীয়তার চেয়ে আইনের যথার্থ ও দ্রুত প্রয়োগের গুরুত্বকে প্রতিষ্ঠা করে এবং বিচার ব্যবস্থার হাস্যকর দীর্ঘসূত্রিতা ও সীমাবদ্ধতারই পরিচয় বহন করে।
সাম্প্রতিক ভারতেও এতদিনকার ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের এই দুনীতিকে ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা তথা হিন্দু মৌলবাদীরা নিজেদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কাজে লাগাচ্ছে, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে দুনীতিমুক্ত প্রশাসনের। ভারতীয় নাগরিকদের একাংশের মধ্যে তাদের প্রভাব বৃদ্ধির পেছনে এটিও অন্যতম ভূমিকা পালন করছে। একই ব্যাপার ঘটেছে আফগানিস্তানে তালিবানদের ক্ষেত্ৰেও। জনসাধারণের বড় একটি অংশ তালিবানদের সমর্থন করছে তাদের কঠোর ইসলামী ফৌজদারি আইন প্রয়োগ করে দুনীতিপরায়ণ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়ার জন্য—যা বিগত প্ৰায় এক দশকে ওখানে প্রায় হয়ই নি। মৌলবাদীরা কিভাবে নানা কৌশলে জনভিত্তি অর্জনের প্রচেষ্টা চালায় তা এ থেকে বোঝা যায়। ফ্যাসিস্টরা ক্ষমতায় আসায় আগে এভাবেই সাধারণ মানুষকে মনোমুগ্ধকর নানা কথাবার্তা দিয়ে মোহগ্ৰস্ত করে,-জার্মানিতে হিটলার যেমন বলেছিল বিশুদ্ধ আৰ্য রক্তের জার্মানজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করার কথা, ভারতে তেমনি বলা হচ্ছে হিন্দুত্ব ও পবিত্র হিন্দু ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার কথা। সঙ্গে উন্নত ও স্বনির্ভর অর্থনীতি থেকে দুনীতিমুক্ত প্রশাসনের আপাত জনস্বার্থবাহী গাজর খাওয়ানোও হয়। এবং এইভাবেই আড়াল করা হয় তাদের ধর্মীয় মৌলবাদী তথা প্ৰগতিবিরোধী, বিজ্ঞান-বিরোধী সাম্প্রদায়িকতাবাদী চরিত্র, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে।
অন্যদিকে আমেরিকা তথা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তালিবানদের প্রচ্ছন্ন সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। কমিউনিজম তথা সাম্যবাদ, সমাজতন্ত্র ইত্যাদির সামান্য পুনরাবির্ভাবকে প্ৰতিহত করতে তারা তালিবানদের ব্যবহার করতে শুরু করেছে। মৌলবাদ ও ফ্যাসিজমের বিরোধিতা, জনগণ ইত্যাদি তাদের কাছে গৌণ।
কিন্তু তালিবানরা কিছু কিছু এলাকায় ক্ষমতায় আসতে না আসতেই তাদের আসল স্বরূপ প্রকাশ করেছে। শুধুমাত্র সমাজের অবিচ্ছেদ্য অর্ধাংশ যে নারী, তাদের উপর নানা কঠোর তালিবানী ফরমান থেকে এর আঁচ পাওয়া যায়।
তালিবানরা মেয়েদের চাকরি করা ও স্কুল-কলেজে যাওয়া নিষিদ্ধ করেছে। মেয়েদের ঘরের মধ্যেই থাকতে হবে, প্রয়োজনে বাজার হাট করতে গেলেও, বোরখা পরে পা-ঢেকে বেরুতে হবে। ইত্যাদি।
একইভাবে পুরুষদের জন্যও আছে কঠোর শরীয়তি আইন; আছে। পশ্চিমী পোষাক পরা, গান, টিভি, ভিডিও ইত্যাদির উপর নিষেধাজ্ঞা, মদ্যপান, ড্রাগ সেবন কিংবা অবৈধ যৌন সম্পর্কের শাস্তি হিসেবে পাথর দিয়ে মেরে ফেলার মধ্যযুগীয় বিধান ইত্যাদি। আসলে হিন্দু-মুসলিম-খৃষ্টান নির্বিশেষে মৌলবাদীদের চিন্তা-চেতনা মানসিকতা সবই মধ্যযুগীয় বা আরো আদিম,-সংকীর্ণতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা, অন্য গোষ্ঠীর প্রতি বৈরিতা, হিংস্রতা ইত্যাদি। মানুষের এইসব পশ্চাদপদ ভাবনাকে ভাঙ্গিয়েই তাদের ক্ষমতা লাভের চেষ্টা।
ধর্মীয় মৌলবাদ সব মিলিয়ে এখনো মানুষের বড় একটি শত্রু। এর সঙ্গে রাজনৈতিক মৌলবাদী মানসিকতা ভিন্নতর বিপদের সৃষ্টি করছে এবং সার্বিক অবস্থাকে জটিলতর করে তুলছে। এ অবস্থায় মানুষের কল্পিত ঈশ্বরের এবং ঐ কল্পনাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নানা প্রতিষ্ঠানিক ধর্মের মূলোচ্ছেদ করার কাজ অতি সক্রিয়ভাবেই পালন করা প্রয়োজন। বড় বেশি প্রয়োজন ‘ধৰ্ম’ থেকে ‘রাজনীতি’ সব ধরনের গোঁড়া মৌলবাদী অন্ধ বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদ করে বিজ্ঞানমনস্কতা অর্জন করার ও মনুষ্যত্বের মুক্তচিন্তাকে সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করার।
———————–
(১) ক্ষমতা পাবার আগেই নিজ সংগঠন বহির্ভূত হিন্দুদের দিয়েও, এ কাজ করা যায়। কিনা তার যাচাই করার রিহার্সেল যথাসম্ভব হয়ে গেল। ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ তারিখে গণেশকে দুধ খাওয়ানোর গণ উন্মাদনা সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে।
(২) শুধু বিজ্ঞান ও ধর্মের মিলনের প্রেসক্রিপশান নয়, পরিবর্তিত সময়ে, আধুনিক মনের গ্রহণযোগ্য করে এই ধরনের লোকেরা হাস্যকরভাবে ধর্মের নতুন নতুন সংজ্ঞাও হাজির করে। যেমন ধর্ম বলতে ঐ পূজা-প্রার্থনা, মন্দির-মসজিদ-গির্জা ইত্যাদি নয়, ধর্ম আসলে মানবিক ঐক্য বা সত্যই আসলে ঈশ্বর ইত্যাদি। তাহলে ঐ ধর্ম, ঈশ্বর এসব কথাকে আঁকড়ে রাখাই বা কেন? এসব গালগল্পও আসলে সূক্ষ্মভাবে ধর্ম ও ঈশ্বরকে টিকিয়ে রাখার মরিয়া চেষ্টা মাত্র। শুধু তাকে একটু মানবিক পালিশ দেওয়া মাত্র।
(৩) মাওসেতুং চীনা পুরুষদের উপর তিন ধরনের আধিপত্যের কথা বলেছিলেন,–(১)রাষ্ট্রব্যবস্থা (রাজনৈতিক কর্তৃত্ব), (২) কুলব্যবস্থা (গোষ্ঠীগত কর্তৃত্ব) ও (৩) অতিপ্রাকৃত ব্যবস্থা (ধৰ্মীয় কর্তৃত্ব) নারীরা এই তিনটির সঙ্গে আরো একটি আধিপত্যের দ্বারা শাসিত–সেটি হল পুরুষদের দ্বারা শাসন (স্বামীর কর্তৃত্ব)।

