- বইয়ের নামঃ ফ্রয়েড প্রসঙ্গে
- লেখকের নামঃদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
- বিভাগসমূহঃ গল্পের বই
০১. অনুবন্ধ – ফ্রয়েড প্রসঙ্গে
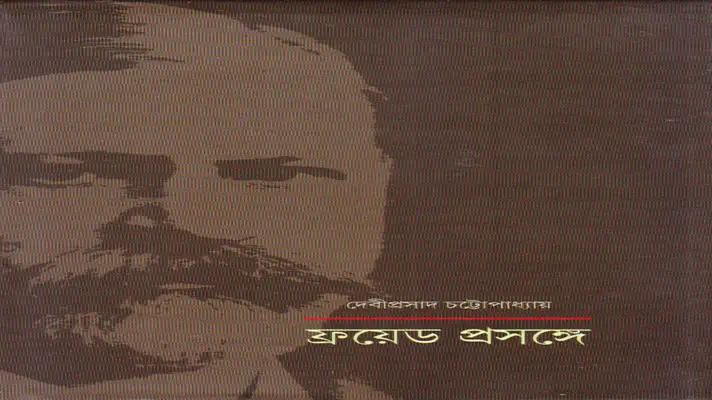
অনুবন্ধ – ফ্রয়েড প্রসঙ্গে
ফ্রয়েডীয় মতবাদের সমর্থনে ফ্রয়েডপন্থীদের পক্ষে এমন এক সুবিধে আছে যা বিজ্ঞানের কোনো ক্ষেত্রে, এমন কি দার্শনিক মতবাদের বেলাতেও, আর কখনো চােখে পড়েনি। সুবিধেটা হলো, বিপক্ষ-সমালোচনার মধ্যে মনোবিকারের লক্ষণ আবিষ্কার করবার দাবি। বিশেষ করে সে-সমালোচনার সঙ্গে যদি কোনো রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের যোগাযোগ থাকে তাহলে তো কথাই উৎসাহের পেছনে মানসিক গরমিলের পরিচয় থাকা সম্ভব, —এবং রাজনীতিটা যদি বৈপ্লবিক হয় তা হলে তার মতে এই সম্ভাবনা প্রায় সুনিশ্চিয়ের কোঠায় পৌঁছোবার কথা।
অথচ, এই বইতে ফ্রয়েডীয় মতবাদের বিবরণ-মাত্র দিতে বসিনি। সমালোচনা করবার প্রয়াসীই হয়েছি। সে-সমালোচনার সঙ্গে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণের যোগাযোগও থাকবে। রাজনীতিটা অহিংস নয়, বৈপ্লবিক। এক কথায় মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মতবাদের দিক থেকে এ-সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করবার যে-দুটি প্রাথমিক দাবি হবে, শুরুতে পূর্বপক্ষ হিসেবে সেই দুটি দাবির জবাব দেওয়া দরকার।
একে একে দুটি কথার আলোচনা করা যাক।
প্রথমত, বিরুদ্ধ সমালোচনার মধ্যে মনোবিকারের লক্ষণ আবিষ্কার করবার দাবি। মনে রাখতে হবে, এ-দাবি একমাত্র ফ্রয়েডবাদেরই। তার মানে, বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং দার্শনিক মত পেশ করবার পর বিরুদ্ধ সমালোচনা—তুমুল সমালোচনা —বহুবারই শোনা গিয়েছে। কিন্তু তার জবাবে এ-কথা। আর কখনো শোনা যায়নি যে, সমালোচকদের এতো যে সোরগোল তা শুধু তঁদের মানসিক গণ্ডগোলেরই পরিচয়। কোপার্নিকাস। যখন প্রথম ঘোষণা করলেন সূর্যের চারপাশেই পৃথিবীর আবর্তন, পৃথিবীকে ঘুরে সূর্যের আবর্তন নয়, তখন কোপার্নিকাসের বিরুদ্ধে সোরগোল খুব কম হয়নি। কিংবা জীবজগতে বিবর্তনের কথা পেশ করবার পর ডারউইনের বিরুদ্ধে তীব্র আর তুমুল সমালোচনার তুফান নিশ্চয়ই উঠেছিল। আজো, লাইসেনকো জীববিজ্ঞানে যে-বিপ্লব, ঘোষণা করেছেন তার বিরুদ্ধে সমালোচনার অন্ত নেই। দার্শনিক মতবাদের বেলাতেও অনেক সময়ই এই রকম। দিদারো, ফয়ারবাখ, এঙ্গেলস—অনেক দার্শনিকের নাম মনে পড়ে। অনেকের বিরুদ্ধেই তীব্র তুমুল সমালোচনা। কিন্তু উত্তরে এ-পর্যন্ত আর কাউকে দাবি করতে দেখা যায়নি যে সমালোচনাগুলি আসলে এক রকমের পাগলামি বিশেষ। বাস্তব দৃষ্টান্ত, বাস্তব অভিজ্ঞতা আর যুক্তিতর্ক দিয়েই বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক সমস্যার কিনারা করবার প্রথা। কিন্তু ফ্রয়েডপন্থীরা শুধু এইটুকুকেই পূর্বপক্ষ-খণ্ডনের একমাত্র পন্থা বলে স্বীকার করতে সম্মত হবেন না। যেমন ধরুন, কেউ হয়তো যে সহজ বৃত্তির কথা উল্লেখ করেন সেটা আসলে অতিকথা মনে এই সহজবৃত্তির উৎপাত নিশ্চয়ই বেশি, তা নইলে একে অস্বীকার করবার এমন উৎসাহ আসবে কোথা থেকে? ঠাকুর ঘরে কে রে-না, আমি তো কলা খাইনি! তর্ক করে সমালোচক হয়তো বলবেন, তা কেমন করে হবে ? নিজের মনেই যদি এ-হেন সহজবৃত্তির উৎপাত থাকতো তাহলে অন্তত নিজে তো তার কথা টের পেতুম! উত্তরে শোনা যাবে, তা হয় না; কেননা, নিজের মনের পুরো খবরটা নিজে নিজে পাওয়া যায় না।
ফ্রয়েদীয় মতবাদের এই বিশেষ সুবিধেটার ভিত্তি ঠিক কী, এইবারে তা স্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যাবে। ভিত্তিটা হলো, আলোচ্য বিষয়ের এক বিশেষ সংজ্ঞা-নিরূপণ। ফ্রয়েড বলেন, নিৰ্জান মন নিয়ে তার আলোচনা, নিজৰ্ত্তান বলতে তিনি বোঝেন মানব-মনের অজানা আর গভীর এক প্রদেশ। তার মানে, ফ্রয়েডের মতে আমরা নিজেরা যথাসাধ্য চেষ্টা করে নিজেদের মন সম্বন্ধে মাত্ৰ সামান্য আর ভাসাভাসা খবর জোগাড় করতে পারি, সেটুকু তাই আমাদের মনের আসল পরিচয় নয়। কেননা আমাদের মনের আসল দিকটার কথা আমরা নিজেরা সব সময় নিজেদের কাছ থেকেই লুকোতে ব্যস্ত। ওই ভাগটারই নাম হলো নির্জন। এবং ফ্রয়েডের মতে আমাদের যা-কিছু চিন্তা, যা-কিছু সচেতন ব্যবহার তার সবটুকুই ওই নির্জনের নিয়ন্ত্রণ মেনে চলে। অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে, নিজৰ্ত্তান মনটা কেন নির্জান ? আমাদের মনেরই প্ৰধান দিক অথচ আমরাই তার খবর পাইনে-এমন ব্যাপার সম্ভব হয় কেমন করে? উত্তরে ফ্রয়েড বলবেন। আমাদের মনের মধ্যে সদা-সর্বদা একটা চেষ্টা রয়েছে ওই নিৰ্ত্তানকে চেপে রাখবার, ওর বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করবার। সেই বাধা উত্তীর্ণ হয়ে নির্জনের বিষয়টুকু সজ্ঞানের স্তরে উঠে আসতে পারে না—দেউড়ির পাহারাদারকে পেরিয়ে যে-রকম মুক্ত রাজপথে বেরিয়ে আসতে পারে না কয়েদখানার বাসিন্দারা। কিংবা পাহারাদারকে ফাকি দিয়ে কয়েদীরা যদি একান্তই বেরিয়ে আসতে চায়, তাহলে তাদের পক্ষে ছদ্মবেশ পরিবার দরকার। আমাদের মনের বেলাতেও ওই রকম : সজ্ঞান সমাজ-বোধের পাহারাদারি পেরিয়ে নিৰ্ভৰ্ত্তানের কথা যদি সজ্ঞানের স্তরে উঠে আসতে চায় তাহলে ছদ্মবেশ ছাড়া গতি নেই। এই-জাতীয় হরেক রকম ছদ্মবেশের বর্ণনা ফ্রয়েডীয় গ্রন্থাবলীতে। দৈনন্দিন খুঁটিনাটির ভুলচুক আর হাসিতামাসা থেকে শুরু করে স্বপ্ন এবং মনোবিকারের লক্ষণ পর্যন্ত কতোই না।