- বইয়ের নামঃ ভাববাদ খণ্ডন – মার্কসীয় দর্শনের পটভূমি
- লেখকের নামঃদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
- প্রকাশনাঃ অনুষ্টুপ (ভারত)
- বিভাগসমূহঃ গল্পের বই
০১. ভাববাদ অনুসারে মানুষের মাথা নেই
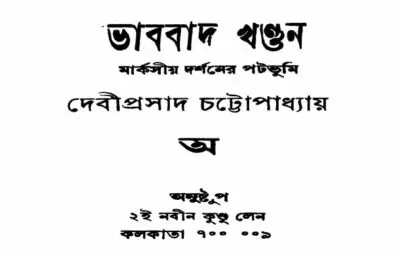
ভাববাদ অনুসারে মানুষের মাথা নেই
ভাববাদ অনুসারে মানুষের মাথা নেই, তবু বুদ্ধি আছে । কথাটা লেনিনের । আজগুবি শোনালেও উপায় নেই, কেননা সহজ কর্মজীবনের কাছে যা আজগুবি ভাববাদ তাকে ভয় করে না । এই মতবাদ অনুসারে বুদ্ধির অতিরিক্ত বাস্তব বস্তু কোথাও কিছু থাকতে পারে না, তাই মানুষের মাথাও নয়। শুধু বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা বা চিন্তা–যে নাম দিয়েই তার বর্ণনা করা যাক না কেন–সবচেয়ে চরম সত্য। ফলে মাথা নেই, তবু বুদ্ধি আছে। লেনিন বলছেন, এ-যেন এক মাথাহীন দর্শন ।
অথচ, দর্শনের ইতিহাসে এমনই রহস্য যে, মাথা বলে কোনো পদাৰ্থ এই মতবাদ অনুসারে বাস্তব না হলেও একে দেখতে লাগে শুম্ভ-নিশুম্ভের সেই পৌরাণিক সেনাপতির মতো-যার মাথা কেটে ফেললেই মরণ হয় না, কাটা মাথা থেকে ছিটকে-পড়া প্ৰত্যেক রক্তবিন্দু জন্ম দেয় এক একটি সমতুল্য দৈত্যের ।
ভাববাদের এই অদ্ভূত লীলাখেলাকে বর্ণনা করতে বসলে দেশ-বিদেশের নানান পৌরাণিক উপাখ্যান মনে ভিড় করতে চায় ; মনে হয় ভাববাদ বুঝি মিশরের সেই পাখি, যুগে যুগে নিজের ভস্মাবশেষ থেকে যে লাভ করে নবজন্ম ; মনে হয় মৃত দেবতার পুনরুজ্জীবন-কাহিনীতেও অবাক হবার কিছু নেই, কেননা দর্শনের পূত মন্দিরে আপাত তেত্ৰিশ কোটি দেবদেবীর মধ্যে যার উপাসনা প্ৰায় তৈলধারার মতো অবিচ্ছিন্ন, তারও মৃত্যুতে জীবনের পরিসমাপ্তি নয়, নবজীবনের সংকেত ।
কেননা, ভাববাদকে বহুবার বহুভাবে খণ্ডন করা হয়েছে। তবুও মরণ হয়নি তার। বরং যাঁরা চণ্ডবিক্রমে একে খণ্ডন করতে এগিয়েছিলেন, তাঁরাই শেষ পর্যন্ত এর মহিমায় পঞ্চমুখ। শুনতে অবাক লাগে, কিন্তু আগেই বলেছি, আজগুবিকে ভিন্ন করলে, আর যাই হোক, ভাববাদকে বোঝবার জো থাকবে না ।
ভাববাদের যেটা মোদ্দা কথা, সহজ বুদ্ধির সঙ্গে সত্যি যে তার মুখ-দেখাদেখি নেই, আর নেই বলে বর্কালির মতো ভাববাদীকে মাথা খুঁড়ে মরতে হয় ভাববাদের সঙ্গে সহজবুদ্ধির সংগতি প্ৰাণপণে প্রমাণ করতে। সহজবুদ্ধির সাধারণ মানুষ মনে করে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে তার সংসার। কিন্তু ভাববাদী বলবেন, সংসার কোথায় ? আছে তো শুধু সংসারের ধারণা। এদিকে, ধারণার দৌলতে সত্যিই সংসার চলে না : পকেট-বোঝাই ধারণাকে উজাড় করে দিলেও মেছুনী এক টিকলি মাছ দেবে না, কিংবা ফাকা দু’নম্বর বাসের ধারণায় চেপে সাড়ে পাঁচটার সময় অফিস-ভাঙা ভিড় এড়িয়ে আরামে বাড়ি ফেরা, হায়, অসম্ভব । উত্তরে ভাববাদী বিরক্ত হয়ে বলবেন, আসলে মাছটাও যে মাছ নয়, বাড়িটাও বাড়ি নয়, মাছের আর বাড়ির ধারণামাত্র । কিন্তু সহজ মানুষ একেবারো যেন নাচারী-মাছের ধারণা খেয়ে পেট নাকি কিছুতেই ভরে না ! ভাববাদী মাথা না মানলেও এমনতর বেয়াদপির কথা শুনে নিশ্চয়ই মাথা গরম করে বলবেন-আসলে পেট বলে জিনিসটেও যে সত্যি নয়, আর পেট ভরানো বলে ব্যাপারটাও যে নেহাত স্থূল কথা, যাকে ধ্রুব সত্য বলা যায়, তা শুধু পেটের ধারণা আর পেট ভরানোর ধারণা ! এহেন চরম জ্ঞানের কথা শুনেও মানুষের মাথা যদি শ্ৰদ্ধায় নুয়ে না পড়ে, তাহলে সন্দেহ করতে হবে যে, ভাববাদীর রকম-সকম দেখে মাথা বলে জিনিসটা সম্বন্ধেই সে শ্ৰদ্ধা হারিয়েছে ।
তাই বলে সমস্ত যুগের সমস্ত দার্শনিকই যে ভাববাদীর এ-সব কথা মাথা পেতে মেনে নিয়েছেন, তাও মোটেই সত্যি কথা নয়। দর্শনের ইতিহাসে ভাববাদ সম্বন্ধে উৎসাহ যতখানি, ভাববাদকে খণ্ডন করবার উৎসাহ বুঝি তার চেয়ে কম নয়। অনেকবার অনেক দার্শনিক ভাববাদকে খণ্ডন করতে চেয়েছেন । কিন্তু, যেটা সবচেয়ে আশ্চৰ্য কথা, শেষ পৰ্যন্ত তাঁরা নিজেরাই ভাববাদের দীক্ষা নিলেন এবং বিধর্মে দীক্ষিত হবার পর যেন হয়ে দাড়ালেন এক একটি মূর্তিমান কালাপাহাড়,–ভাববাদেরই চরম নৃশংস প্রচারক। ভাববাদ তাই মরেও মরে না, যমালয় থেকে ফিরে আসে নতুন বর নিয়ে, নচিকেতার মতো । একদিকে ভাববাদকে তীব্র, তীক্ষ্ণ আক্রমণ, অপরদিকে সেই ভাববাদের কাছেই করুণ আত্মসমৰ্পণ । এ-কথা যে-সব দার্শনিকের সম্বন্ধে সত্য, তাদের “দুর্বলচেতা” বলে উড়িয়ে দিতে যাওয়া নেহাত আত্মপ্ৰবঞ্চনা হবে । কেননা, দর্শনের ইতিহাসে তাঁরাই হলেন দিকপাল-বিশেষ। স্বদেশে শঙ্কর, প্ৰাচীন গ্রীসে সক্রেটিস, আধুনিক যুরোপে কাণ্ট এবং সাম্প্রতিক যুগে অভিজ্ঞতাবিচারবাদীদের (Empirio-Critics) থেকে শুরু করে প্রয়োগবাদী (Pragmatists), বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী (Realist) ) পৰ্যন্ত-যুগে যুগে এঁরাই তো যুগান্তকারী দার্শনিক বলে স্বীকৃত । অথচ এঁরা সকলেই প্ৰবল উৎসাহে ভাববাদকে খণ্ডন করার পর প্রবলতর উৎসাহেই ভাববাদের মাহাত্ম্যে মেতে উঠেছেন ।
আচাৰ্য শঙ্করের “বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন” ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে সুপ্ৰসিদ্ধ ! ( প্ৰাচীন ভারতীয় দর্শনের পরিভাষায় “বিজ্ঞান’ শব্দটার অর্থ হলো মনের ধারণা, Science নয় ; তাই বিজ্ঞানবাদ আসলে আমরা যাকে ভাববাদ বা Idealism বলে উল্লেখ করছি তাইই। বৌদ্ধ দার্শনিকদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় ছিল, যার নাম বিজ্ঞানবাদী এবং যার মতবাদ-ও এমন-কী যুক্তি-প্ৰায় হুবহু য়ুরোপীয় দার্শনিক বার্কলির মতোই ) । এই বিজ্ঞানবাদকে খণ্ডন করতে বসে শঙ্কর, আর যাই হোক, তথাকথিত বৈদান্তিকসুলভ নিম্পূহ সংযমের পরিচয় দেননি, এমন-কী তাঁর ভাষার সহজ প্ৰসাদগুণকে ছাপিয়ে উঠেছে প্ৰত্যক্ষ বিতৃষ্ণ । শঙ্কর বলেন, বিজ্ঞানবাদীর দল যে এমনতর আজগুবি কথা বলতে সাহস পায়, তার আসল কারণ তাদের মুখের মতো অঙ্কুশ নেই ! অর্থাৎ অঙ্কুশের ভয় থাকলে অমন নির্লজ্জ মিথ্যে বলতে তারা সাহস পেত না । শঙ্কর বলছেন, বহির্জগৎকে উড়িয়ে দেবে কেমন করে ? তার অনুভূতি যে অবিসংবাদিত ! দিব্বি এক পেট খেয়ে এবং রীতিমতো পরিতৃপ্ত হয়ে যদি কেউ বলে “কিছুই তো খাইনি, কই পরিতৃপ্তও তো হইনি,”–তাহলে তার কথা যে-রকম মিথ্যে হবে, সেইরকমই মিথ্যে বিজ্ঞানবাদীর কথা । ইন্দ্ৰিয়ের সঙ্গে বহির্বস্তুর সন্নিকর্ষ হবার পর, এবং স্বয়ং অব্যবধানে বহির্বস্তুকে অনুভব করার পর, বিজ্ঞানবাদীও বলে “বহির্বস্তু যে কী, কই তা তো জানি নে, কখনো তা দেখিনি–মনের বাইরে সত্যি কিছু নেই।” বিজ্ঞানবাদীর দল নিজেদের কথাটা হয়তো আর একটু শুধরে নিয়ে বলবে, বিষয়ের অনুভূতিকে আমরা অস্বীকার করতে যাব কেন, আমরা শুধু অস্বীকার করি তার বাহ্যত্বরূপ-বিজ্ঞেয় পদার্থরাশি অন্তর্বর্তী ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। উত্তরে শঙ্কর বলছেন, এ হলো গায়ের জোরের কথা । অনুভূতির সময় আমরা তো এই বলেই অনুভব করি।– এটা হলো স্তম্ভ, ওটা হলো কুড্য । কই এমন তো কখনো অনুভব করিনে যে, এটা হলো স্তম্ভের মানস রূপ, ওটা হলো কুড্যর মানস-রূপ ! তাছাড়া, বহির্বস্তু বলে কোনো জিনিস। যদি কোথাও কোনোকালে না থাকে, তাহলে অন্তর্বর্তী ধারণাকেই বা কেমন করে “বহির্বৎ” হিসাবে অনুভব করা সম্ভব ? আসলে, “বহির্বৎ” বলে ধারণাটা এল কোথা থেকে ? এমন কথা তো মুখ-ফুটে কেউ বলতে পারে না যে, বিষ্ণুমিত্রের চেহারাটা ঠিক বন্ধ্যাপুত্রের মতো !