ইতিহাসের আলোকে আত্ম-দর্শন
মুঘল-পূর্ব যুগের ভারতের মুসলিম শাসকরা পরিচিত ছিলেন তুর্ক বা তুরুক নামে। এঁদের অবশ্য স্বতন্ত্র গোত্রীয় ও দৈশিক নাম ছিল, যেমন খালজি, তুঘলক, লোদী, উজবক, আইবক, ঘোরী প্রভৃতি। তাঁরা যেমন একগোত্রীয় ছিলেন না, তেমনি তারা এক অঞ্চল থেকেও আসেননি। মধ্য এশিয়ার ও আফগানিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলে ছিল তাদের বাস।
মুঘল-পূর্ব যুগে ভারতীয় ভাষায় ও সাহিত্যে প্রায় সর্বত্রই এঁদেরকে তুর্ক বা তুরুক বলে অভিহিত করা হয়েছে; জাতি-পরিচয়ে কোথাও মুসলমান বলে উল্লেখ করা হয়নি। কেবল ধর্ম প্রসঙ্গে মুসলমান বলে আখ্যাত হয়েছেন। পরবর্তীকালেও মুঘল, ইরানী, হারুই, বলখী, খোরাসানী, পার্সী, বোখারী, সমরখন্দী, কাশঘরী, তাব্ৰেজী, কুনিয়া, কাবুলী, পর্তুগীজ, ইংরেজ, ফিরিঙ্গি, আমানীয়, ওলন্দাজ, দিনেমার, হার্মাদ, ফরান্সিস প্রভৃতি নিবাসগত নামই পাই। অতএব মধ্যযুগে জাতি-পরিচয় ছিল দেশগত-ধর্মগত নয়। হিন্দু ও হিন্দুস্তানী পরিচয়ও দেশগত। এও বলা চলে বিদেশীরা এভাবেই এদেশে পরিচিত হত।
প্রমাণে ও অনুমানে বোঝা যায়, দেশজ মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির ফলেই ধর্মভিত্তিক জাতি পরিচয় শুরু হয়। এবং তা মুঘল আমলেই বহুল প্রচলিত হয়। তখন থেকেই ভারতের হিন্দু মুসলমানের দুর্ভাগ্যের শুরু। কেননা, ধর্মচেতনা প্রবল হলে চৈত্তিক সংকীর্ণতা প্রশয় পায়। স্বধর্মী না হলেই মানুষকে পর ভাবা, শত্রু মনে করা এবং অবিশ্বাস করা ধার্মিক মানুষের প্রায় স্বভাবসিদ্ধ। এই হিন্দু-মুসলমান-শিখ পরিচয়ের প্রাবল্যবশে মুঘল আমলেই শুরু হয় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও বৈর, দাঙ্গা ও হাঙ্গামা। ইংরেজ আমলে শাসক-শাসিতের সম্পর্ক যখন ঘুচে গেল, তখন সমকক্ষতার ঔদ্ধত্যে ও দ্বান্দ্বিক স্বার্থের প্ররোচনায় লোভের ও লাভের বৈষম্যে এই বিরোধ ও বিবাদ বেড়ে চলে এবং স্বাধীনতা-উত্তর যুগে তা বর্বর পাশবিক মত্ততার রূপ ধারণ করে। নরহত্যার বীভৎসতা তাদের মনে উল্লাস জাগায়।
এ ব্যাপারে মুসলমানদের দুর্ভাগ্য ও দুর্ভোগই অধিক। একে তো ভারতরাষ্ট্রে তারা সংখ্যালঘু ও হিন্দুর অনুগ্রহজীবী, তার উপর মিথ্যা পরিচয়ে তারা হিন্দুর প্রতিহিংসাবৃত্তির শিকার। মধ্য এশিয়ার ও আরব-ইরানের বহুলোক শাসক ও শাসক-সহচর রূপে ভারতে আসলেও তাদের সংখ্যা এখনকার মুসলমানদের শতকরা তিনজনের বেশি যে নয় তা নিঃসন্দেহে বলা চলে। কেননা যেসব দেশ থেকে মুসলমান শাসকরা এসেছে, সেখানেও জনসংখ্যা আজো বেশি নয়। এই ধর্মভিত্তিক পরিচয়ের ফলে দেশী মুসলমানেরা কিছুটা মিথ্যা গৌরব লাভের দুর্বলতা বশে এবং কিছুটা আত্মপরিচয় বিস্মৃতির দরুন এই বিদেশী শাসক ও শাসক সহচরদেরকে নিজেদের জ্ঞাতি ভাবতে অভ্যস্ত হয়। এভাবে তাদের নিন্দা-গৌরবের ভাগীও হয়ে যায়। বিদেশী, বিজাতি ও বিধর্মী শাসকের বিরুদ্ধে হিন্দুদের যে স্বাভাবিক ক্ষোভ ও বিরূপতা ছিল, ইংরেজ আমলে জাতীয়তাবোধ বিকাশের ফলে তা তাদের মনে তীক্ষ্ণ ও তীব্র হয়ে উঠে এবং সাহিত্যে, ইতিহাসে ও রাজনীতিতে বিষবৃক্ষ জন্মাতে থাকে। আত্মবিস্মৃত দেশী মুসলমান যেমন তুর্কী-মুঘলদের নিন্দা-গৌরবকে নিজেদের বলে ভাবে, তেমনি তুকী-মুঘল শাসকের প্রতি অমুসলমানদের আরোপিত ও উচ্চারিত কলঙ্ক আর নিন্দাও তাদের গায়ে লাগে। তারা গায়ে মাখে বলেই হিন্দুরাও তাদেরকেই তুর্কী-মুঘলের বংশধর বলে জানে এবং পুরোনো পীড়ন ও ক্ষোভ স্মরণ করে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠে।
আজকের সংখ্যালঘু ভারতীয় মুসলমানের দুর্ভাগ্যের ও দুর্ভোগের অর্ধেক কারণ এ-ই। এই মনস্তাত্ত্বিক আধি থেকে সাধারণ হিন্দুর মুক্তিলাভের আশু-সম্ভাবনা কম। কাজেই ত্রস্ত ও নির্যাতিত ভারতীয় মুসলমানের যন্ত্রণা দীর্ঘস্থায়ী হবে। তাদের ত্রাণপথ দৃষ্টি-সীমার মধ্যে নেই। পাকিস্তানেও হিন্দুনিধন হয়েছে, তবে তা সবসময় প্রতিশোধমূলক। উত্তেজনার কারণ ঘটিয়েছে ভারত। ভারতে হাজারোর্ধ্ব বার বড়-ছোট মুসলিম হত্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এক্ষেত্রে পাকিস্তান অনুপম সংযম ও সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছে। পাকিস্তানে অর্থাৎ পূর্ব বাঙলায় প্রতিশোধমূলক দাঙ্গা হয়েছে মাত্র চারবার কী পাঁচবার এবং নিজেরা বাধিয়েছে দুবার। এ তারতম্যের কারণও হয়তো শাসক জাতির অভিমান-পুষ্ট মুসলিম-মনে হিন্দু-বিদ্বেষের অভাব।
তাছাড়া ব্রিটিশ আমলে হিন্দুদেরকে ধনে-মানে-বিদ্যায় উন্নত দেখেও অশিক্ষিত দরিদ্র মুসলমান তাদেরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখত, সেই শ্রদ্ধার রেশও উত্তেজনা প্রশমনে কার্যকর হয়েছে। আবার দক্ষিণ ভারতে মুসলমানের সংখ্যা নগণ্য, তাই সেখানে হিন্দুরা মুসলমানকে প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করে না। তাদের বর্তমান অস্তিত্ব গ্রাহ্যের মধ্যে নয় বলেই হিন্দুরা তাদের প্রতি উদাসীন, তাই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে না। একই কারণে খ্রীস্টান কিংবা পাসীরাও নির্বিঘ্ন। কিন্তু উত্তর ভারতে মুসলিম সংখ্যা নগণ্য নয়, আর দিল্লী-কেন্দ্রী মুসলিম শাসনের স্মৃতিও হিন্দুমনে অম্লান। কাজেই পূর্বের লাঞ্ছনা-স্মৃতি, সম্পদ-লোভ এবং জীবিকার ক্ষেত্রে বর্তমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা উত্তর ও মধ্য ভারতীয় হিন্দুমনে মুসলিম নিধনে ইন্ধন যোগায়। এছাড়াও ধনে-জনে হৃতসর্বস্ব উদ্বাস্তুদের প্রতিহিংসাপরায়ণতা ও অসহিষ্ণুতা এবং জীবিকাসমস্যাও উত্তরভারতে ঘন ঘন মুসলিম-হত্যায় প্ররোচনা দান করে। এর উপর সুবিধাবাদী রাজনীতির খেল তো রয়েইছে।
.
০২.
তুর্কী-মুঘল ও আরব-ইরানীর জ্ঞাতিত্ববোধ অন্যদিকেও মধ্যবিত্ত দেশী মুসলমানের সমূহ ক্ষতি করেছে। তারা নিজেদের চিরকাল স্বদেশে প্রবাসী ভেবেছে। তারা অনুকরণ করেছে বলখী বোখারীর, স্বপ্ন দেখেছে আরব-ইরানের, অনুসরণ করেছে দেশ-কাল-প্রতিবেশহীন জীবন-পদ্ধতি। তারা প্রতিবেশের অনুগত করে জীবন রচনায় ব্রতী হয়নি। এই প্রতিবেশিক প্রয়োজনের অস্বীকৃতিতে তাদের জীবন ছিন্নমূল ও কৃত্রিম হয়ে পড়েছিল। তাই বিগত হাজার বছরের মধ্যে জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই দেশজ মুসলমানের উচ্চমানের কোনো অবদান প্রত্যক্ষ নয়। যে-মাটিতে তারা লালন পেয়েছে, সে মাটিকে তারা ভালবাসেনি। ধাত্রীরূপেও গ্রহণ করেনি। ইসলাম গ্রহণের পরে মধ্যবিত্ত দেশজ মুসলমানের দৃষ্টি আর কখনো মরুভূ আরব ও সরাব-সাকীর ইরান অতিক্রম করে স্বদেশে ফিরে আসেনি। তাই উনিশ শতকে ও বিশ শতকের গোড়ার দিকে মুসলিম লিখিয়ে আঁকিয়েদের আলোচ্য ও অনুধ্যেয় বিষয় ছিল ইসলামপূর্ব ও ইসলাম-উত্তর যুগের আরব-ইরানী পুরাণ, ঐতিহ্য, ইতিহাস ও দর্শন। হাফিজ জালন্ধরী, ফররুখ আহমদ অবধি সে-ধারা রয়েছে আজো অব্যাহত।
এই পদ্মা-কোকিলের দেশের মানুষ চোখ-কান বন্ধ করে রূপ দেখে বসোরাই গোলাপের, গান শোনে নাইসাপুরী বুলবুলের। বিন্ধ্য-হিমালয়ে তাদের মন ভরে না, হেরা-সিনাই-তুরে তাদের আকর্ষণ, আম-কলা-কাঠালে তাদের রুচি নেই, আরবি খেজুরে তাদের লোভ, দেশের শ্যাম নীলিমায় তারা ক্লান্ত, সাহারা তাদের মন ভোলায়। অমুসলিম হাতেম-নওশেরোয়া-রুস্তম তাদের আত্মীয়, পর হল কর্ণার্জুন-যুধিষ্ঠির। এমনি বিকৃত মন-বুদ্ধি দ্বারা চালিত হয়েছিল বলে তারা স্বস্থ ও সুস্থ ছিল না। বাস্তবকে তারা অবহেলা করেছিল, কিন্তু স্বপ্নও ছিল অনায়ত্ত। যদি দেশ-কাল প্রতিবেশের প্রয়োজনানুগ জীবন-ভাবনায় তারা ব্ৰতী হত, তাহলে তারা স্বস্থ ও সুস্থ জীবনের ফসলে ভরে তুলতে পারত তাদের জগৎ। তাতে তাদের মানস-জগৎ হত প্রশস্ত, চিত্তলোক হত আলোকোজ্জ্বল, গড়ে উঠত তাদের স্বকীয় একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। জীবনে, সাহিত্যে, দর্শনে তাদের অবদান হত গৌরবের ও গর্বের। স্বধর্মীর ইতিহ্য-গৌরবের সন্ধানে রিক্তচিত্তে কাঙালের মতো স্পেন থেকে গোবী মরু অবধি এমনি মানস-বিচরণের প্রয়োজন হত না। আধুনিক আরব, ইরান, মধ্য-এশিয়াও নয়, মধ্যযুগের মধ্য-এশিয়ায় ও মধ্যপ্রাচ্যে আজো তারা আওয়ারা হয়ে শক্তি, আদর্শ, ঐশ্বর্য ও প্রেরণার খোঁজে ঘুরে বেড়ায়। তারা বাস করে একালে, ধ্যান করে অতীতের, স্বপ্ন। দেখে মরুভূর।
.
০৩.
আরো বড় বিড়ম্বনার কথা, যে-তুকী-মুঘলের জাতিত্ত্ব-স্বপ্ন দেশজ মুসলমানদেরকে চেতনার ক্ষেত্রে দেউলে করেছে, সে-তুর্কী-মুঘল শাসকগোষ্ঠী কখনো দেশী মুসলমানকে আপনজন ভাবেনি। অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যই করেছে চিরদিন। তারা ছিল ঐশ্বর্যের উল্লাসে, প্রতাপ ও প্রভাবের দাপটে, আভিজাত্যের গর্বে, উপভোগের আনন্দে ও প্রতিপত্তির গৌরবে আকাশচারী। দেশী মুসলমানের সঙ্গে তাদের স্বাভাবিক কোনো সামাজিক ও বৈবাহিক সম্পর্ক ছিল না। দেশী খ্রীস্টান ও ইংরেজের মতোই ছিল সর্বব্যাপারে স্বাতন্ত্র্য। তারা তুর্কী-মুঘল শাসকের অনুগ্রহে আর্থিক ক্ষেত্রে উপকৃতও হয়নি। বড় চাকরিগুলো পেত বিদেশাগত মুসলমানেরা। এ পার্থক্য মুঘল আমলের শেষ দিন অবধি বর্তমান ছিল। তারা এদেশকে ও দেশের মানুষকে স্বদেশ ও স্বজাতি বলে গ্রহণ করেনি। সাতশ বছর শাসন-শোষণ করেও তারা এদেশকে মনে করত দারুল হর। অতএব দেশী মুসলমানকে তারা ইংরেজ যেমন করত দেশী খ্রীস্টানকে–কী অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্যই না করত! তুর্কী-মুঘলের জাতিত্বগবী উত্তরভারতীয় আজকের মুসলমানদের বাঙালির প্রতি অবজ্ঞার মধ্যে রয়েছে সেই পুরোনো স্মৃতির রেশ। তার প্রমাণ পাই এক ঐতিহাসিক দলিলে। ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদাবাদ দরবারের পদস্থ মুসলিম কর্মচারীরা মেজর মুনরোর সঙ্গে ষড়যন্ত্রমূলক চুক্তি সম্পাদনের জন্যে চুক্তিপত্রের যে-খসড়া তৈরি করেছিল, তার দু-একটি শর্ত এখানে উদ্ধৃত করছি। এতে বোঝা যাবে মুসলিম শাসকগোষ্ঠী সাতশ বছর পরেও বিদেশী শাসক-শোষকই থেকে গিয়েছিল। অবশ্য মুহম্মদ তুঘলক, ফিরোজ তুঘলক, শেরশাহ্ এবং আকবর ও জাহাঙ্গীর এর ব্যতিক্রম।
The company should in every respect regard as its own the honour and reputation of the Mughals who are strangers in this country and make them its confederates in every business. Whatever mughals whether Iranis or Turanis come to offer their services should be received on the aforesaid terms…. [ and that] should anyone be desirous of returning to his own country… he should be discharged in peace. (Quotation from Foot note 5. (pp. 12-13)] India, Reza Khan maintained. as a Dar-ul-Harb. (Reza Khans notę, Francis MSS. (I.O) Eur E 13 P. 417) He obviously shared the current notion of the Muslim Rulers in India, To whom it was not strictly a Dar-ul-Islam a muslim homeland. Muslims living in Hindustan (that is, North India) did so according to the same notion, as rulers or as sojourners only)–Calender of Persian Correspondence Vol. 1. No. 2423. Quoted by Dr. abdul Majed Khan in The transition in Bengali. (1765-75A. D.) P.12, and see also his Foot note 5. at PP. 12-13* [*পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।]
অথচ বাঙালি তথা ভারতীয় মুসলমানরা সিরাজদ্দৌলা, মীর কাসিম, টিপু ও বাহাদুর শাহ্ ওয়াজেদ আলির জন্যে পরম মমতায় ও চরম আত্মীয়তাবোধে কী কান্নাটাই না কাঁদে! দেশী মুসলমান যে বাদশাহর জাত ছিল না এবং মুঘল-শাসনের অবসানে তারা যে রাজ্যহারাও হয়নি, এ সত্য যতদিন উপলব্ধি না করবে, ততদিন তারা আত্মস্থ হবে না এবং আত্মত্রাণ, আত্ম-নির্মাণ ও আত্মোন্নয়নের সত্য ও সুষ্ঠু পথও তারা খুঁজে পাবে না।
এ সূত্রে মুঘলদের দুর্ভাগ্যের কথাও মনে জাগে। পারস্য রাজ্যের সহায়তায় দিল্লীর সিংহাসন ফিরে পেয়েছিলেন হুমায়ুন। সেই কৃতজ্ঞতায় ও অনুরাগে হুমায়ুন ইরানীদের চাকুরির আকারে আশ্রয় ও প্রশয় দিতে থাকেন। জাহাঙ্গীরের আমল থেকে শাহ আলমের কালাবধি বৈবাহিক ও সাংস্কৃতিক সূত্রে রাজ্যে ও রাজকার্যে ইরানী প্রভাব ও প্রতাপ পূর্ণতা পায়। এসব লোক ব্যক্তিগত লাভ ও লোভকেই জীবনের পরম ও চরম লক্ষ্য করে নিয়েছিল। এদের সঙ্গে জুটেছিল মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার আরো বহু গোত্রীয় মানুষ। ভারত ছিল তাদের চোখে সম্পদ আহরণের নির্বিঘ্ন ক্ষেত্র। রাজা ও রাজসরকারের সঙ্গে তাদের কোনো মমতার সম্পর্ক ছিল না। আনুগত্য ছিল চাকুরিগত। তাই দুর্বল বাদশাহর অক্ষমতার সুযোগে তারা মুঘল সাম্রাজ্য ভাগ করে নিল।
মুঘল বাদশাহরা যদি স্বগোত্রীয়দের উপর নির্ভর করতেন, তাহলে গোত্র-স্বার্থেই সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব সাধনে তারা যত্ন করত। কাজেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের মূলে ছিল অমুঘল শাসক ও সেনাপতির আধিক্য। এরা সাম্রাজ্যের সঙ্কটকালে স্ব স্ব স্বার্থে দায়িত্ব ও কর্তব্যভ্রষ্ট হয়ে আনুগত্য প্রত্যাহার করেছিল। এখানে ইবন-খালদুনের কথা মনে পড়ে। তিনি বলেছেন, কৌমচেতনা ও কৌমের সঙ্ঘবদ্ধ প্রয়াসেই রাজশক্তির উদ্ভব, বিকাশ ও স্থিতি সম্ভব হয়। এবং সাম্রাজ্যের আয়ত্তাতীত ভৌগোলিক বিস্তৃতি, রাজ-পরিজনের বিলাসিতা, কৌম-চেতনায় শৈথিল্য ও আলস্য, ভিন্ন গোত্রীয় লোকদের শাসনকার্যে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ প্রভৃতিই রাজবংশের পতনের মুখ্য কারণ। অন্তত মুঘল সাম্রাজ্য বিলুপ্তির ক্ষেত্রে উক্ত কারণগুলি সত্য হয়ে উঠেছিল।
এখানে উল্লেখ্য যে, ইবন খালদুনের আমলে রাষ্ট্রিক জাতীয়তার উন্মেষ হয়নি। তাই তিনি গোত্র ও কৌম-চেতনার কথা বলেছেন। এ যুগে হলে তিনি দৈশিক কিংবা রাষ্ট্রিক জাতীয়তাবাধ ও দেশপ্রেমের অভাবই দেশ বা জাতির রাষ্ট্রিক-পতনের কারণ বলে নির্দেশ করতেন।
পরিশিষ্ট
কৌতূহলী পাঠকের জন্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের পূর্ণ বিবরণ সম্বলিত অংশ এখানে উদ্ধৃত হল :
Calender of Persian Correspondence.
1764, Sept. 22.
2416. Zainul-abidin Khan to Major Munro. Has received through Asad khan his letter desiring the writer to joint the English army with as many able-bodied and well-mounted Moghals, Turanis, etc as possible. Although it is dishonourable for all men, particularly for men of family, to desret the service they are engaged in and go over to their Masters enemies, yet there are several reasons which justify such conduct in the Moghals. First, the Wazir, not withstanding his oath upon the Quarn, murderd the Nawab Muhammad Quli Khan, who was the glory of the Moghals, and who to the writer was dearer than a father or a brother. Secondly, the Wazirs behaviour to the Nawab Mir Qasim, who is a descendant of the Prophet, has been very shameful. It is not allowed by any religion that a person, who flees to another for protection with his family and effects, even if he be a person of low rank, should meet with treatment other than friendly. Why then has he in violation of his oath and agreement behaved in such a manner as to incur universal censure and reflect disgrace upon the Moghal name? Thirdly, he has never failed to break every engagement he has entered into and every oath he has taken. Fourthly, neither he nor his ministers pay any regard to his own sign-manual. Fifthly, with regar to the Moghals, who are starngers in this country, and who, having nothing to depend upon but their monthly pay, are brought ot distress whenever that is stopped, he thinks of nothing but how to oppress and ruin them. Moreover, he takes no notice of men and family, but places all his confidence in low and worthless people. Sixthly, he by no means makes a proper distinction between his friends and his enemies, but makes a practice of countenancing the latter and ill-treating the former. The assisting and supporting of such an oppressor is neither conformable to reason, nor to the Quran, nor to the rules of any religion, and the quitting of his service can reflect no dishonour upon anyone either in the sight of God or man. There fore if the English, who are celebrated for thir Justice and good faith, are desirous of an alliance with the Moghals, and are willing to agree to their just demands and swear to the observance of the agreement by the names of Jesus and Mary, and if the gentlemen of the Council put their seals to it and speedily forward it, a great number of Moghals and Turanis will without delay join the English army. Praises Ali Riza Khan and desires the Major to invite him back to the English service. Assures him that the .said Khan was carried away to the Wazirs camp, contrary to his own inclinations, by his troop of horse and the people of Tikari, that inspite of his Highnesss solicitations, he has refused to enter his service, that he has been greatly oppressed on account of his connection with the English, and that he is sincerely attached to them. Refers him to Mirza Iwaz Beg for particulars. (Trans P. L. R., 1759-64, No. 239. p.p. 476-478. Abs. P. L. R, 1759-65. P. 85.
Sept. 22.
2418. Zainul-abidin Khan to Asad Khan. Has received his letter together with Major Munros letters for the writer and Muhammad Baqir Khan. The Moghals, who have all been informed of the addressees commands, met and unanimously resolved to draw up a treaty and send it to him for his approval and for transmission to the gentlemen of the English council, that they may set their seals to it and swear to the observance of it upon the Bible and in the name of the Prophet Jesus and the Prophet Mary. God forbid that in the service of the English, the Moghals should meet with the same treatment as in that of the Wazir, and that when their business is done, they should be turned away, remote as they are from their native country and brouht to shame and distress. The addressee is a chief of the Moghals and a man of family and understanding. He should settle matters to his satisfaction. Whatever staisfies him, will satisfy the writer. And Whatever satisfies the writer, will satisfy all the Moghals. The merit or demerit of whatever may be done will be attributed to the writer, and the writer, before God, The prophet, and the common father of the Moghals, will attribute it all to the addressee. Desires that the territory by the Ganges and the Jumna may be made over to the Moghals rent-free. Mirza Taqi Khan, Muhammad Baqir Khan, Ali Riza Khan, Rustam Beg, Baba Beg Khan, Muhammad Taqi Khan, Muhammad Tahir Beg, Masum Ali Beg and all the other chiefs have empowered the writer to act for them. Mirza Muhammad Hasan is also ready to join in the conspiracy. Has heartily engaged himself in this dangerous business, Which may be the cause of much bloodshed. Ali Riza Khan has refused to enter the Wazirs service, although His Highness has offered him Rs. 1,000 a month besides a present of Rs. 2,000, which is more than he gives to any of his officers. Requests the addressee to prevail upon the English to invite him back to their army. Requests him also not to invite Mirza Mahdi Ali Khan to join the Moghals, lest he should take the first place. Will rejoice at the addressees elevation to the Nizamat of Oudh, irrespective of whether he is favourable to the writer or not, as it will conduce to the happiness of thousands of people, and as the interest of one individual must not be put in competition with that of the public. He is a man of understanding, but as the writer is more advanced in years, he takes the liberty of advising him that he should not do anything that may lessen him in the estimation of the English, who are men of penetration and foresight; and whose undertaking are conducted with wisdom. Requests to be favoured with a speedy reply. Refers him to Mirza Iwaz Beg for other particulars. PS. Requests him to procure as soon as possible a line or two from Major Munro to Rustam Beg Afshar and Baba Beg Khan, who are both men of consideration among the Moghals. (Trans. P.L.R., 1763 64, NO. 241, PP. 480-483. Abs P.L.R., 1759, P. 85).
Sept. 22. 2423. Paper of articles sent by the Moghals to Major Munro.
(1) The Company should in every respect regards as its own the honour and reputation of the Moghals, who are strangers in this country, and make them its confederates in every business. (2) They should be granted a proper place in the country of the habitation of their families and dependendants. (3) Whereas sixty rupees a month have been fixed for all but Jamadars, Hawaldars, and Dafahdars, there are several privates who have always been distinguished and have received from one to three hundred rupees a month. These men should be allowed something more than what they received in the Wazirs army. (4) Whatever Moghals, whether Iranis or Turanis come to offer their services, they should be received on the aforesaid terms. Moreover, a present of Rs. 100 per head should be immediately given them and a months pay advanced them. (5) At present there should not be raised any difficulties as to the size of horses. (6) Whenever a Moghal is killed in battle or dies a natural death, his son or relation should be received in his place. (7) As several men are in debt, a small sum of money should be sent to enable them to discharge their debt. (8) Should anyone be desirous of returning to his own country, his arrears should be immediately paid and he should be discharged in peace. (Trans. P.L.R. 1763-64, NO. 246, pp. 491-492)
Sept. 22
2424. Shah Mal, Qaladar of Rohtas, to Major Munro. Has answered his several letters. Remains firm in the fort in the hope of his favour and protection. Mir Sulaiman has arrived at Batein (?) fort in Akbarpur, idly relying upon his Highnesss deceitful promises of kindness and reward. But he has been plainly told that the people of Rohtas fort will by no means submit to the Wazir, Whose behaviour to the Nawab Ali Jah (Mir Qasim) has not been such as to make them believe that it will be for their interest to do so. Hopes that the Major will send some assistance as soon as possible. Numbers of the enemys troops are coming towards Rohtas. Some have already arrived at Tilloot, while other are stationed at Sasaram. If he is not speedily supported, he has no expectations but of becoming a sacrifice. Has already sent a paper of requests. Desires that an agreement properly executed and assuring him of protection may be sent. Desired also that some money may be granted to the people of the fort. They are now the companys servants, and any disgrace that they may suffer, will fall upon the English. .
(Trans. P.L.R, 1763-64, No. 247, pp, 486-488. Abs. P.L.R, 1759-65, : p. 83)
Sept. 22
2424A. Shah Mal, Qal-adar of Rohtas, to Major Munro. Has received his letter agreeing to set his hand to the writers paper of requests, but saying that Mir Asad Ali, the bearer of it, has not yet arrived. Encloses another paper. Although he is fully satisfied with what the Major has said in his letter, yet in compliance with the custom of the world, he requests that the paper will be properly signed, sealed and speedily sent to Rohtas together with some money and a body of troops. The enemys troops, which were at Tilloot, have scattered themselves on every side. Should they surround the fort, the garrison will be greatly distressed for want of provision. Makes repeated appeals for help. Refers him to Mir Asad Ali and Dr. Fullarton for particulars. (Trans. P. L. R, 1763-64, No. 248, pp, 488-490. Abş. P.L.R. 1759-65, p. 84)
N.B : Abbreviations.
Abs. P.L.R. Represents the volume of Abstracts of Persian Letters received.
Trans. P. L. R.– Represents the volume of Translations of Perisian letters received.
ইতিহাসের ধারায় বাঙালি
০১.
আমাদের দেশের নাম বাঙলা দেশ, তাই ভাষার নাম বাঙলা এবং তাই আমরা বাঙালি। আমরা এদেশেরই জলবায়ু ও মাটির সন্তান। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই এদেশের মাটির পোষণে, প্রকৃতির লালনে এবং মানুষের ঐতিহ্য-ধারায় আমাদের দেহ-মন গঠিত ও পুষ্ট। আমরা আর্য নই; আরবি, ইরানী কিংবা তুর্কিস্তানীও আমরা নই। আমরা এদেশেরই অস্ট্রিক গোষ্ঠীর বংশধর। আমাদের জাত আলাদা, আমাদের মনন স্বতন্ত্র, আমাদের ঐতিহ্য ভিন্ন, আমাদের সংস্কৃতি অনন্য।
.
০২.
আমরা আগে ছিলাম animist,পরে হলাম Pagan, তারও পরে ছিলাম হিন্দু-বৌদ্ধ, এখন আমরা হিন্দু কিংবা মুসলমান। আমরা বিদেশের ধর্ম নিয়েছি,ভাষা নিয়েছি, কিন্তু তা কেবল নিজের মতো করে রচনা করবার জন্যেই। তার প্রমাণ নির্বাণকামী ও নৈরাত্ন-নিরীশ্বরবাদী বৌদ্ধ এখানে কেবল যে জীবনবাদী হয়ে উঠেছিল, তা নয়; অমরত্বের সাধনাই ছিল তাদের জীবনের ব্রত। বৌদ্ধচৈত্য ভরে উঠেছিল অসংখ্য দেবতা ও উপদেবতার প্রতিমায়। হীনযান-মহাযান ত্যাগ করে এরা তৈরি করেছিল বজ্রযান-সহজযান, হয়েছিল থেরবাদী। এতে নিহিত তত্ত্বের নাম গুরুবাদ।
এই বিকৃত বৌদ্ধ জীবন-চর্যায় মিলে এদেশের আদিবাসীর জীবন–তত্ত্ব ও জগদ্দর্শন। এদেশের মানুষ চিরকাল এই কাদামাটিকে ভালবেসেছে, এর লালনে তার দেহ গঠিত ও পুষ্ট, এর দৃশ্য তার প্রাণের আরাম ও মনের খোরাক। সে এই আশ্চর্য দেহকেই জেনেছে সত্য বলে, দেহস্থ চৈতন্যকে মেনেছে আত্মা বলে-পরমাত্মারই খণ্ডাংশ ও প্রতিনিধি বলে। তাই চৈতন্যময় দেহ তার কাছে মানুষ আর দেহ বহির্ভূত অখণ্ড চৈতন্য হচ্ছে তার কাছে মনের মানুষ, রসের মানুষ কিংবা ভাবের মানুষ।
সে জীবনবাদী, তাই বস্তুকে সে তুচ্ছ করে না, ভোগে নেই তার অবহেলা। তাই জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে যা কর্তব্য, তাতেই সে উদ্যোগী। সেজন্যেই সে তার গরজ মতো জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তার দেবতা সৃষ্টি করেছে। পারলৌকিক সুখী জীবনের কামনা তার আন্তরিক নয়– পোশাকীই। তাই সে মুখে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যবাদ গ্রহণ করেছিল, অন্তরে কোনদিন বরণ করেনি। তার পোশাকী কিংবা পার্বণিক জীবনে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম এবং আচার আবরণ ও আভরণের মতো কাজ দিয়েছে, কিন্তু তার আটপৌরে জীবনে ঠাই পায়নি। সে জানে, চৈতন্যের অবসানে এ দেহ ধ্বংস হয়, চৈতন্যের স্থিতিতে এ দেহ থাকে সুস্থ, স্বস্থ ও সচল। তাই সে দেহকে জেনেছে কালস্রোতে ভাসমান তরী বলে। প্রাণকে বুঝেছে শ্বাস-প্রশ্বাসের যন্ত্র বলে আর চৈতন্যকে মেনেছে মন বলে। তাই এই জীবনটাই তার কাছে মন-পবনের নৌকার চলমান লীলা রূপে প্রতিভাত হয়েছে, কাজেই পার্থিব জীবনই তার কাছে সত্য এবং প্রিয়। জীবনের জীবন অর্থাৎ ইহলোকে ও পরলোকে প্রসারিত জীবন তার কল্পনায় দানা বেঁধে উঠতে পারেনি কখনো। তাই বৈরাগ্যে সে উৎসাহ বোধ করেনি, বাউলেরা তাই গৃহী, যোগীরা তাই অমরত্বের সাধক।
তার দর্শন সাংখ্য, তার শাস্ত্র যোগ। তাই দেহতত্ত্বই তার সাধ্য। বৌদ্ধ তান্ত্রিক, হিন্দু তান্ত্রিক এবং মুসলমান সুফীরা এদেশের এই ঐতিহ্যই নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করেছিলেন। চর্যাপদে, বৈষ্ণব সহজিয়া পদে, বাউল গানে, বৌদ্ধ বজ্র-সহজ-কালচক্র ও মন্ত্রনে, শৈব-শাক্ত সাহিত্যে, বাউল সুফী সাহিত্যে আমরা দেহকেন্দ্রী তত্ত্ব ও সাধনার সংবাদই পাই! ইতিহাস বলে বৌদ্ধধর্ম এখানে যক্ষ-দানব-প্রেত ও দেবতা-পূজায় রূপান্তরিত হয়েছিল। সেনদের নেতৃত্বে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত উত্তর ভারতিক ব্রাহ্মণ্যবাদ এখানে কার্যত টেকেনি। আদিবাসী বাঙালির জীবন-জীবিকার মিত্র ও অরি দেবতা–শিব, শক্তি (কালী),মনসা, চণ্ডী, শীতলা, ষষ্ঠী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ প্রভৃতিই পেয়েছেন পূজা।
ওহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনের পূর্বে শরীয়তী ইসলাম এখানে তেমন আমল পায়নি। এখানে ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করেছেন পাঁচগাজী ও পাঁচপীর। নিবেদিত চিত্তের ভক্তি লুটেছে খানকা, অর্ঘ্য পেয়েছে দরগাহ্ আর শিরনি পেয়েছেন সত্যপীর-জাফর-ইসমাইল-খান জাহান-গাজীরা কিংবা বদর-বড়খা-সত্যপীর। এদের কেউ পাপ-পুণ্য তথা বেহেস্ত-দোজখের মালিক নন, তাহলে এদের খাতির কেন? সে কী পার্থিব জীবনের সুখ ও নিরাপত্তার জন্যে নয়?
কেবল এখানেই শেষ নয়, বিদ্রোহী বাঙালি, নতুনের অভিযাত্রী বাঙালি নব-নব চিন্তার দিগন্ত প্রসারিত করে চলেছে চিরকাল। বৌদ্ধযুগের শীলভদ্র, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ, মীননাথের কথা কে না জানে? সেন আমলের জীমূতবাহনের মনীষা আজো বিস্ময়কর, নব্যন্যায় ও স্মৃতি বাঙালি মনীষার গৌরব-মিনার। চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না,মানবিক বোধের ও মনুষ্যত্বের সুউচ্চ বেদীতে দাঁড়িয়ে যিনি মানুষের মর্যাদার ও মানবিক সম্ভাবনার বাণী উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করে গেছেন, যিনি স্থূল চেতনার বাঙালিকে সূক্ষ্ম জীবনবোধে উদ্বুদ্ধ করে তার চেতনার দিগন্ত প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। সাম্য ও প্রীতির সুমহান মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে বাঙালি চিত্তে মানব-মহিমা-মুগ্ধতার বীজ বপন করেছিলেন তিনি। তার পরেও রামমোহনের মনীষা ও মুক্তবুদ্ধি এক সঙ্কট থেকে, এক আসন্ন অপমৃত্যু থেকে সেদিন হিন্দুকে রক্ষা করেছিল; মুসলমান পেয়েছিল পরোক্ষ ত্রাণের পথ। তারও আগে পাই সত্যপীর-কেন্দ্রী মিলন-ময়দানের সন্ধান, আর পাই বাউলের উদার : মানবতাবোধ। এভাবে দেশকালের প্রতিবেশে বাঙালি যুগে যুগে নিজেদের নতুন করে রচনা করেছে, গড়ে তুলেছে নিজেদের কালোপযোগী করে।
মনে রাখা প্রয়োজন, বাঙালির বীর্য বর্বর লাঠালাঠির জন্যে নয়, তার সংগ্রাম নিজের মতো করে বেঁচে থাকার। নিজের বোধ-বুদ্ধির প্রয়োগে নিজেকে নতুন নতুন পরিস্থিতিতে নতুন করে গড়ে তোলার সাধনাতেই সে নিষ্ঠ। এসব তার সে-সাধনারই সাক্ষ্য ও ফল।
.
০৩.
ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন তার স্বতন্ত্র জীবন-বোধের ও মননের মৌলিকতার স্বাক্ষর রয়েছে, রাজনৈতিক জীবনেও তেমনি রয়েছে তার বিশিষ্ট মনোভঙ্গির সাক্ষ্য।
সে চিরকালই শোষণ ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, তাই উত্তরভারতীয় গুপ্ত শাসনে সে স্বস্তি পায়নি। এজন্যেই গুপ্তদের পতনের পর শশাঙ্কের নেতৃত্বে বাঙালি একবার জেগে উঠেছিল। মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল তার আত্মসম্মানবোধ। গুপ্ত যুগের বদ্ধবেদনা ও সঞ্চিত গ্লানি প্রতিহিংসার আগুনে নিঃশেষ হতে চেয়েছিল। এরই ফলে স্বাধীন ভূ-পতি বঙ্গ-গৌরব শশাঙ্ককে দেখতে পাই উত্তর-ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদী রাজা হর্ষবর্ধনের প্রতিদ্বন্দ্বীর ভূমিকায়।
তারপর একদিন বাঙালির ভাগ্যে দীর্ঘস্থায়ী সৌভাগ্য-সূর্যের উদয় হয়েছিল। আমরা পাল রাজাদের কথা বলছি। স্মরণ করুন সেই গৌরবময় দিন, যেদিন ভারতের মাটিতে প্রথম গণতান্ত্রিক চিন্তার বীজ উপ্ত হয়েছিল। প্রজারা যেদিন গোপালকে রাজা নির্বাচিত করেছিল, সেদিন এই বাঙালির জীবনে মননে ও সংস্কৃতিতে এক নতুন অধ্যায় হয়েছিল শুরু। স্বাধীনতার স্বস্তি তার জীবনে সেদিন যুগদুর্লভ স্বপ্ন জাগিয়েছিল। বাঙালির হৃদয় সেদিন নব-সৃষ্টির উল্লাসে মেতে উঠেছিল, চঞ্চল হয়ে উঠেছিল নব অনুভবের আবেগে। তার চিত্তলোক আন্দোলিত হয়েছিল নবীন জীবন-চেতনায়– জন্মলগ্নের বেদনায় সদ্য উন্মোচিত জীবনবোধের রূপায়ণ-প্রেরণায় সে ছুটেছিল আদর্শের সন্ধানে। যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপাল গীতি তারই প্রতীকী রচনা। মানুষের চেতনার রাজ্যে–আদর্শ লোকের চিরন্তন প্রশ্নের গভীরতম সমস্যার সমাধানে সেদিন বাঙালি-মনন জয়ী হয়েছিল। তার সিদ্ধান্তে ভুল ছিল না। সে ত্যাগের নয়, ভোগেরও নয়, গ্রহণ করেছিল মধ্য পন্থা- Golden mean। ত্যাগ তার লক্ষ্য নয়, নিছক ভোগ তার কাম্য নয়, পার্থিব জীবনের সার্থকতার পথই তার বাঞ্ছিত। পরলোকের মিথ্যা আশ্বাসে সে বিধাতার সৃষ্টির জাগতিক জীবনের মহিমা খর্ব করতে চায়নি, কিংবা ভোগের পক্ষে ডুবে কলঙ্কিত করেনি জীবনকে। পৃথিবীকেই সার জেনে, জীবনকে সত্য মেনে, মাটিকে ভালবেসে সে জীবনের বিচিত্র রস আহরণ করতে চেয়েছে, উপলব্ধি করতে চেয়েছে জীবনের প্রসাদ। এজন্যে তার লক্ষ্য হয়েছে জীবন-বৃক্ষে ফুল ফোঁটানো, ফল ফলানো। এরই মধ্যে সে সমাজকে ভেবেছে উদ্যানরূপে, সংস্কৃতিকে জেনেছে সিঞ্চিত জল হিসেবে, ঐতিহ্যকে বরণ করেছে সার বলে। সেদিন বাঙালির আত্মোপলব্ধির জন্ম হয়েছিল, জীবন-ধারণায় তার মুক্তি ঘটেছিল, পেয়েছিল সে যথার্থ, চলার পথের সন্ধান। তাই পাল আমল ছিল বাঙালির জীবনে ও বাঙলার ইতিহাসে সোনার যুগ। ধনে, ঐশ্বর্যে, সংস্কৃতিতে, সম্ভ্রমে, চেতনায় ও চিন্তায় বাঙালি সে গৌরব, সে-সুখ, সে-আনন্দ পরে অনেক অনেক কাল আর পায়নি।
সব সুদিনের শেষ আছে। মৃত্যুর বীজ ঢোকে দেহে, তা-ই একদিন অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হয়ে ঘটায় মৃত্যু। পালদেরও পতন হল শুরু। তার কারণ সে স্বাজাত্য ভুলল। হারাল আত্মবিশ্বাস, ছাড়ল অভিমান। শেষের দিকে বৌদ্ধ পাল রাজারা নিজেদের উদার সংস্কৃতি ছেড়ে উত্তরভারতীয় বর্ণাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুরাগী হয়ে উঠলেন। ব্রাহ্মণ্য প্রভাব ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে উঠল। ব্রাহ্মণ্যবাদ আবার জনপ্রিয় হল। বৌদ্ধমত ত্যাগ করে লোকে ব্রাহ্মণ্য মত গ্রহণ করতে লাগল। সে-সূত্রে বাঙালির দৃষ্টি হল বহির্মুখী। পতনের বীজ উপ্ত হল এভাবেই। স্বাজাত্যবোধ গেলে সহধর্মিতা ও সহযোগিতা যায় উবে। অনেকতায় আসে অনৈক্য। সমস্বার্থ ও অভিন্ন আদর্শের প্রেরণা না থাকলে বাঁধন যায় টুটে। সেদিন বাঙালির সোনার যুগ এভারে হল অবসিত।
সেনদের পিতৃপুরুষের নিবাস ছিল দাক্ষিণাত্যেকাটে। হয়তো তাঁরা ছিলেন দ্রাবিড়। পাল রাজত্বের অবসানে তাঁরা হলেন দেশপতি। কিন্তু বাঙালির সঙ্গে ছিল না তাদের আত্মার যোগ। উত্তরভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির তাঁরা ছিলেন ধারক ও বাহক। কল্যাণবোধে নয়, ধর্মীয় গোঁড়ামি বশেই বাঙলাকে ও বাঙালিকে তারা উত্তরভারতীয় আদলে গড়ে তুলতে হলেন প্রয়াসী। এই কৃত্রিম প্রয়াসে তারা বাহ্যত সফল হলেন বটে, কিন্তু আত্মার ঐশ্বর্য হারাল বাঙালি। জীর্ণতা তার আত্মার কন্দরে বাঁধল বাসা। বাইরের আয়োজন-আড়ম্বর অন্তর্লোক করে দিল দেউলিয়া। তাই ধোয়ী, জয়দেব, হলায়ুধ মিশ্রের চোখের সামনে পালাতে হল লক্ষ্মণ সেনকে।
রাজার সঙ্গে ছিল না প্রজার যোগ। স্বাজাত্যর অছেদ্য বন্ধন হয়েছিল শিথিল। তাই রাজার দুর্ভাগ্যে বিচলিত হয়নি প্রজারা। নতুন অধিপতিকে ছেড়ে দিল রাজ্য-পাট।
বিদেশী-বিভাষী তুর্কীরা দখল করে নিল এদেশ। কিন্তু তারা নিজেদের স্বার্থেই চাইল স্বাধীন হতে। বাঙালির তাতে ছিল সায়। কেননা, বাঙালির ধন তাহলে তেরো নদীর ওপারে দিল্লীর ভাণ্ডারে যারে না। তুর্কীদের প্রতি বাঙালি বাড়াল সহযোগিতার হাত। তুর্কীরা লড়ল দিল্লী-পতির সাথে। বহু জয়-পরাজয়ের পর অবশেষে ১৩৩৯ থেকে ১৫৩৮ সন অবধি স্বাধীন সুলতানী আমলে বাঙলা আর্থিক সৌভাগ্যসমৃদ্ধির গৌরব-গর্ব অনুভব করবার সুযোগ পেল। বিদেশাগত হলেও তখন সুলতানরা স্বাধীন ছিলেন বলে রাজস্ব মোটামুটি দেশেই খরচ হত। কিন্তু ১৫৩৯ সনে শেরশাহের গৌড় বিজয় থেকে বাঙলার দুর্ভাগ্যের সূচনা হয়। শূরেরা প্রায় বাইশ বছর বাঙলা দেশ শাসন করলেন বটে, কিন্তু তারা ছিলেন বিহারী এবং বহিবঙ্গীয় স্বার্থ, বিশেষ করে আফগান স্বার্থরক্ষা করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। আফগান কররানীরা ছিল ক্ষমতার লড়াইয়ে ব্যস্ত এবং ১৫৭৫ সনে আকবর জয় করে নিলেন বাঙলা দেশ। তেরো নদীর ওপারের দিল্লীর বাদশাহর রাজত্বে ও রাজস্বে যত আগ্রহ ছিল, তার কণা পরিমাণও ছিল না বাঙালির জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তাব্যবস্থায় উৎসাহ।
তাছাড়া আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে ১৬২৪ সন অবধি বাঙলায় এক রকম অরাজকতাই চলছিল। অবাঙালি বংশোদ্ভব স্থানীয় সামন্তরা প্রায় বিয়াল্লিশ (১৬১৭ সন অবধি) বছর ধরেই মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে লড়েছেন। তারা মুঘলের অধীনতা সহজে স্বীকার করতে চাননি, ফলে একরূপ দ্বৈতশাসনই চলেছিল–যার স্বরূপ ছিল পীড়ন ও লুণ্ঠন। তাছাড়া মুঘল সেনানীদের মধ্যেও ছিল অন্তর্বিরোধ ও বিদ্রোহ। তবু সেদিন পুরোনো সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করে বাঙালিরা এই বিদেশী সামন্তদের হয়ে সংগ্রাম করেছিল বাঙলার স্বাধীনতা এবং বাঙালির স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যে। সামন্তদের ঐক্যের অভাবে বাঙালির সে প্রয়াস সেদিন ব্যর্থই হয়েছিল।
মোটামুটিভাবে বলতে গেলে ১৬২৪ থেকে ১৭০৭ সন অবধি বাঙলায় মুঘল শাসন দৃঢ়মূল ছিল। কিন্তু সেনানী ও বেনে-সুবেদারের শাসনে বাঙলা উপনিবেশের দুর্ভোগই কেবল বেড়েছে। ত, র উপর বাঙালিকে বইতে হয়েছিল আসাম, কোচবিহার ও চট্টগ্রাম অভিযানের বিপুল ও ব্যর্থ ব্যয়ভার। মুঘল-শোষণ ছাড়াও য়ুরোপীয় বেনেদের শোষণে তখন দেশে আকাল। এদিকে ষোলো শতকের প্রথম পাদ থেকে পর্তুগীজ দৌরাত্মের শুরু, তার চরম রূপ দেখা দেয় সাজাহান-আওরঙ্গজেবের শাসনকালে। সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রজার জীবন ও সম্পদ রক্ষার দায়িত্ব যেন তাদের নয়, কেবল রাজস্বের অধিকারই তাদের। তাই বিদেশী বেনের একচেটিয়া বাণিজ্য, মঘ-হার্মাদের লুণ্ঠন, সুবাদারের ঔদাসীন্য সেদিন বাঙালিকে ধনেও কাঙাল, মনেও কাঙাল করে ছেড়েছিল।
বিজাতি-শাসিত বাঙালির দেউলিয়া জীবনের সাক্ষ্য মেলে তাদের চিন্তার দৈন্যে, সাংস্কৃতিক জীবনের নিষ্ফলতায় ও রুচির বিকাশে এবং ধর্মবোধের নতুনত্বে। সেদিন অসহায় বাঙালি আস্থা হারিয়েছিল পুরোনা ধর্মবোধে; ছেড়েছিল মন্দির, মসজিদ। জীবন ও জীবিকার ধাঁধায় পড়ে বিভ্রান্ত বাঙালি সন্ধান করেছিল নতুন ইস্ট দেবতার–যারা পার্থিব জীবনে দেবেন দুর্লভ সুখ ও আনন্দ, আনবেন প্রাচুর্য ও নিরাপত্তা। সেদিন বিমূঢ় বাঙালি বৃহৎ ও মহতের আদর্শ ও আকাক্ষা কত ক্ষোভ ও হতাশায় না ত্যাগ করেছিল! সেদিন তার সর্বোচ্চ আকাক্ষা ছিল: আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে। মুর্শিদকুলি-আলিবর্দীরা বাঙালির সে ক্ষুদ্রতম আকাক্ষাও সেদিন মেটানোর গরজ বোধ করেননি। তাই মুঘল যুগের শুরু থেকেই দুর্দিনের যে দুর্যোগ নেমে এসেছিল, তার ফলে সত্যপীর-সত্যনারায়ণ-কেন্দ্রী ইষ্টদেবতার পূজা-শিরনির মাধ্যমে নিপীড়িত নিঃস্ব হিন্দু-মুসলমান এক মিলন-ময়দানে এসে জমায়েত হয়েছিল। বল-বীর্য তাদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না আর। কেবল প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে তারা সত্যপীর-সত্যনারায়ণ, দক্ষিণ রায়-বড়খগাজী, কালুরায়-কালুগাজী, বনদেবী-বনবিবি, ওলাদেবী-ওলাবিবি, ষষ্ঠীদেবী-ষষ্ঠীবিবির পূজা-শিরনি দিয়েই স্বস্তি খুঁজছিল।
১৭০৭ সনে আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে বাঙালির আর্থিক অবস্থার আরো অবনতি হয়েছিল, মুর্শিদকুলি খাঁর নতুন রাজস্বব্যবস্থায় প্রজা-শোষণ বেড়েছিল। কেননা তিনি মধ্যস্বত্বভোগী ইজারাদারদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করতেন। তার জামাতা সুজাউদ্দীন এবং দৌহিত্র সরফরাজ খাঁ ছিলেন দুর্বল শাসক। সামন্তরা হয়ে উঠলেন এ সুযোগে প্রবল। আলিবর্দী এদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেই হলেন বাঙলার নওয়াব। এজন্যে এদেরকে শাসনে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাছাড়া তাঁর- ষোলো বছরের নওয়াবীকালে বারোটি যুদ্ধও করতে হয়েছিল। ফলে দেশে শোষণ-পীড়ন বেড়ে গেল। মারাঠার সঙ্গে লড়াই করার জন্যে সেদিন আলিবর্দী একজন সেনাপতিও পেলেন না তার সামন্ত সিপাহীর মধ্য থেকে। কিশোর সিরাজুদ্দৌলা হলেন সেনাপতি। যুদ্ধ-প্রহসনের পরে আলিবর্দীকে ছাড়তে হল উড়িষ্যা, দিতে হত বারো লক্ষ টাকা চৌথ। এভাবে মারাঠা শক্তিকে ঠেকিয়ে তিনি আরো কিছুকাল নওয়াবী করলেন!
কালের চাকা স্থির ছিল না। এই কুশাসন ও চরিত্রহীনতার পরিণাম সমাজের সর্বস্তরের দেখা দিল দুষ্টক্ষতরূপে। যুদ্ধ, ছল-প্রতারণা ও লুণ্ঠন-শোষণে মানুষের জীবন জীবিকায় এতটুকু নিরাপত্তা ছিল না। ব্যবসা-বাণিজ্যে হাত ছিল না দেশের লোকের, বৃদ্ধি পেয়েছিল রাজস্বের হার। বেনিয়া দালালের দৌরাত্ম্যে ঘরেও স্তস্তি ছিল না লোকের। অভাব, পীড়ন ও অনিশ্চয়তায় জনগণের দুঃখের ভরা হয়েছিল পরিপূর্ণ।
তারপরে পলাশীর প্রহসনে বদল হল শাসক, পালটে গেল নীতি, পরিবর্তিত হল রীতি আর দ্বারে এল নতুন যুগ। বিশ্বাসভঙ্গে মীরজাফরের সহযোগী ও সমকক্ষ এবং জামাতা মীর কাসেম আলি খাঁ ঘুষে-লব্ধ নওয়াবী করতে গিয়ে টের পেলেন নিজেদের অবস্থা। কিন্তু তখন অনেক দেরি। হয়ে গেছে। জাল তখন ইংরেজ প্রায় গুটিয়েই এনেছে। ফদের দোর বন্ধ, কাজেই পরিণামে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই ছিল না তার ভাগ্যে।
ইংরেজ বেনেরা স্থিরই করতে পারল না পঁচিশ বছর ধরে শাসন করবে কী শোষণ করবে!
ফলে ১৭৯৩ সন অবধি চলল একপ্রকারের দ্বৈত-অদ্বৈত শাসন, যার ফলে দেশে অরাজকতা, লুণ্ঠন, পীড়ন চলছিল অবাধে। এর মধ্যেই ঘটেছিল খণ্ড প্রলয়ের চেয়েও ভয়াবহ মন্বন্তর–ছিয়াত্তরের মন্বন্তর যার নাম। এ কেবল দুর্ভিক্ষ নয়– মহামারী, সে মহামারী অপমৃত্যু ঘটিয়েছিল দেহের–মনের আত্মার। মনুষ্যত্ব সেদিকার বাঙলায় ছিল অভাবিত সম্পদ।
অবশেষে বেনেবুদ্ধির জয় হল। কোম্পানি স্থির করল তারা শাসনও করবে, শোষণও করবে। ১৭৯৩ সন থেকে সুপরিকল্পিত ব্যবস্থায় শাসন-শোষণ হল শুরু।
এর মধ্যে বাঙালি মুসলমানরা ওহাবী-ফরায়েজী প্রভৃতি ধর্মান্দোলনের মাধ্যমে আযাদী আন্দোলনও চালাতে চেয়েছিল। মজনু শাহর ফকিরদল ছিল মূলত Saboteurs গেরিলাযোদ্ধা। ১৭৬০ সন অবধি এসব বিপ্লব চলছিল।
.
০৪.
কিন্তু তখন বিপর্যস্ত জীবনে শিথিল চরিত্র জনগণের পক্ষে সে আহ্বানে সাড়া দেওয়া সম্ভভ ছিল না। উত্তর ভারতের সৈয়দ আহমদের পরামর্শে ১৮৬০ সনের পর থেকে মুসলমানরা বৃটিশ-প্রীতিকেই নীতি হিসেবে গ্রহণ করে। ১৯৪৭ সন অবধি অধিকাংশ ইংরেজি-শিক্ষিত মুসলমানের রাজনৈতিক চেতনা চাকরির ক্ষেত্রে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষের রূপ নেয়। এর মধ্যে আযাদীকামী স্বস্থ মুসলমানরা ও চাকরির প্রত্যাশাহীন মোল্লা-মৌলানারা কংগেসের মধ্যেমে সংগ্রাম চালিয়ে যান। আর অন্যেরা মুসলিমলীগের মাধ্যমে আর্থিক স্বাচ্ছল্য লাভের প্রচেষ্টায় ব্রতী হলেন হিন্দুদের সঙ্গে। দ্বন্দ্ব জিয়ে রেখে। এই সংগ্রাম মূলত হিন্দু জমিদার, মহাজন ও অফিসবাবুর বিরুদ্ধেই। তখন মুসলমান মাত্রেরই এই তিন শত্রু ইংরেজ নয়। কিন্তু হিন্দু-বিরল অঞ্চলের অর্থাৎ সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ কিংবা বেলুচিস্তানে মুসলিমদের হিন্দুবিদ্বেষ তেমন ছিল না, যেমন ছিল না মুসলিম-বিরল দাক্ষিণাত্যের হিন্দু-মনে মুসলিম-বিদ্বেষ।
রাজনীতির ক্ষেত্রে মুসলিম জনগণের এই ক্ষোভের সুব্যবহার হয়েছিল মুসলিম লীগের পতাকাতলে হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চলের মুসলমানরা সমবেত হল ইংরেজ তাড়াবার জন্যে নয়–হিন্দুর থেকে সম্পদ ও চাকুরির অধিকার ছিনিয়ে নেবার উত্তেজনায়। এটিই কালে কালে পৃথক ধর্ম, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জাতিত্বের প্রলেপে পুষ্ট ও প্রবল হয়ে মুসলমানদের স্বতন্ত্রসত্তার স্বীকৃতিতে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র লাভের উদ্দীপনা ও অনুকুল পরিবেশ তৈরি করেছিল। মুসলিমলীগ যে বৃটিশবিরোধী ছিল না এবং কংগ্রেস যে স্বাধীনতাকামী ছিল, তার প্রমাণ কংগ্রেসীদের জেলে যেতে হয়েছে, মুসলিম লীগ কর্মীরা কখনো বৃটিশের কোপদৃষ্টি পায়নি।
.
০৫.
কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের জন্ম বাঙলায়। কিন্তু বাঙালির হীনমন্যতা এবং কিছুটা উদারতার জন্যে, দুটোই হল হাতছাড়া।
এগুলোর নেতৃত্ব ও সাফল্যের কৃতিত্ব পেল অবাঙালিরা। অথচ পাকিস্তান এল বাঙালির আন্দোলনে, স্বাধীনতাও এল ১৯৪২ সনের বাঙালির আগস্ট-আন্দোলন প্রভৃতির প্রভাবে। ১৯৪৬ সনের কলকাতার দাঙ্গা, তার প্রতিক্রিয়ায় বিহার-ননায়াখালির হাঙ্গামাই স্বাধীনতা ও পাকিস্তান প্রাপ্তি ত্বরান্বিত করেছিল। আজকে যেসব অঞ্চল পাকিস্তানভুক্ত, সেদিন বাংলাদেশ ছাড়া আর কোথাও মুসলিমলীগ প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি, অথচ মুসলিমলীগের মাধ্যমে অর্জিত পাকিস্তানের মা-বাবা আজ সেসব অঞ্চলের লোকই। কেবল কী তা-ই? বাঙালির দেশপ্রেম ও রাষ্ট্রিক আনুগত্যেও সেসব মোড়ল মুরুব্বিদের সন্দেহের অন্ত নেই। এর চেয়ে বড় বিড়ম্বনা কল্পনাতীত।
অবশ্য বাঙালির এ ক্ষতি বাঙালির দালাল-নেতাদেরই দান। পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুরাষ্ট্রের নামে সর্বপ্রকার বঞ্চনা হল শুরু।
সৈন্য বিভাগে বাঙালি দেড় লক্ষ চাকুরির হকদার। হীনমন্যতাগ্রস্ত বাঙালির কাছে সেদিন সে অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি উচ্চারণও ছিল অশোভন ও অযৌক্তিক। পাঞ্জাব-করাচী-বোম্বাইয়ের মুসলমানরা পাকিস্তানের অর্থনীতির চাবিকাঠি রাখল নিজেদের হাতে। অর্থাগমের পথ রইল আগলে। ব্যবসা-বাণিজ্য-কারখানা রইল তাদেরই খপ্পরে। কেরানীগিরিতে ও তার উপরি প্রাপ্তিতেই বাঙালি রইল কৃতাৰ্থমন্য হয়ে।
আগে পদ ও পদবি লোভে দালালি করে, পরে প্রসাদ-বঞ্চিত হয়ে বিরোধী দলে যোগ দিয়ে এসব দালাল-নেতারা মায়াকান্না শুরু করে দেয় জনগণের জন্যে, মুখস্থ ফিরিস্তি দেয় অবিচারের, ছদ্ম সংগ্রাম চালায় বাঙালির অধিকার আদায়ের।
বাঙালির থেকে সংখ্যাসাম্য নীতির স্বীকৃতি আদায় করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে একক প্রদেশ গঠন করে শহীদ সোহরাওয়ার্দী বাঙালির যে ক্ষতি করেছেন তার তুলনা বিরল।
রাজনীতি ক্ষেত্রে ফজলুল হকের সুবিধাবাদ-নীতি বাঙালি রাজনৈতিক কর্মীদের করেছে আদর্শভ্রষ্ট ও চরিত্রহীন। স্বার্থান্বেষী জনপ্রতিনিধিরা আজ এ-দলে, কাল ও-দলে থেকে দেশের, গণমানুষের ও গণচরিত্রের যে ক্ষতিসাধন করেছেন, তা আমাদের উত্তরপুরুষের কালেও পূরণ হবে কী না সন্দেহ।
পাবলিক সার্ভিস কমিশনে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা পরিষদে, মন্ত্রিসভায় কখনো বাঙালির অভাব ছিল না, কিন্তু তাদের দান কি, প্রয়াসের ফল কি? কেউ কখনো জিজ্ঞাসা করে না।
জাতীয় সঙ্গীত হচ্ছে বল, বীর্য, প্রেরণা ও আদর্শের উৎস। আমাদের সেই জাতীয় সঙ্গীত রচিত হয়েছে জনগণের অবোধ্য ফরাসি ভাষায়। অধিকাংশ পাকিস্তানীর প্রাণের যোগ নেই সে কওমী সঙ্গীতের সঙ্গে। খেতাবের ভাষাও ফরাসি। কয়জন বোঝে তার গুরুত্ব? সর্বত্রই এমনি বিড়ম্বনা।
পাকিস্তানের কোনো অঞ্চলের ভাষাই উর্দু নয়। চল্লিশ-পঞ্চাশ জন উত্তরভারতীয় Civilian এবং লিয়াকত আলির প্রভাবে ও দাবীতে দেশবহির্ভূত ভাষা উর্দু পেল পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার অধিকার ও মর্যাদা। অথচ যে-স্তরেই থাকুক পাকিস্তানের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষাও মাতৃভাষারূপে আজো প্রীতি ও পরিচর্যা পাচ্ছে এবং সেই প্রবণতাই লক্ষণীয়রূপে বাড়ছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মাতৃভাষা না হলে যে কোনো বিদেশী ভাষাই টিকে থাকতে পারে না, তার বড় সাক্ষ্য রয়েছে এদেশের ইতিহাসে। তুর্কী-মুঘল-ইরানীর প্রতিপোষণ পেয়েও এদেশের এককালের রাষ্ট্রভাষা ফরাসি তার অস্তিত্ব হারাল। কেননা এটি সাম্রাজ্যের কোনো অঞ্চলের লোকেরই মাতৃভাষা ছিল না। শাসক হয়েও সংখ্যালঘু বলেই শাসকেরা তাদের মাতৃভাষা তুর্কীও ধরে রাখতে পারেননি। তাই কারো প্রীতির পরিচর্যা সে ভাষা পায়নি। ফলে মৃত্যুই ছিল তার অনিবার্য পরিণাম। উর্দুরও সে পরিণাম সম্ভব ও স্বাভাবিক। তবু ইতিহাসের সাক্ষ্য তুচ্ছ জেনে আমরা কোমর বেঁধে লেগেছি প্রচারে। উত্তরভারতীয় Civilian কিংবা তাদের উত্তরপুরুষের প্রভাবের আয়ু কয়দিন! সিন্ধি, বেলুচী, পশতু ও সারাইকীভাষীরা যখন ঐ Civilian-দের আসন এবং শাসনের দণ্ড ধারণ করবে, কোন্ মমতায় তারা বিদেশী উর্দুর লালনে উৎসাহ রাখবে? কাজেই অবিলম্বে উর্দু চালু না হলে, অদূর ভবিষ্যতে ভাষিক-দ্বন্দ্ব ভারতের মতো তীব্র হয়ে দেখা দেবে।
ইসলাম ও মুসলিম জাতীয়তার ভাঁওতা দিয়ে অগ্রগতির পথরুদ্ধ করে দেশী-দালালের মাধ্যমে পাঞ্জাবীরা ও করাচীওয়ালারা আর কতকাল এখানে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ চালাবে–এ জিজ্ঞাসার অবকাশ রাষ্ট্রের পক্ষে কল্যাণকর নয়। স্বস্বার্থে মানুষ বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে মারামারি করে, কেবল ইসলামী ভ্রাতৃত্বের দোহাই দিয়ে দুর্বলকে বঞ্চিত ও শোষণ করা কতকাল সম্ভব!
অর্থনৈতিক কারণেই তো অধিকার-বঞ্চিত মুসলমানরা স্বতন্ত্র জাতীয়তার ধুয়া তুলে পাকিস্তান চেয়েছিল। নানা অজুহাতে পাক-ভারতে সংখ্যালঘু হত্যার পশ্চাতেও এই সম্পদ-সংগ্রহের অবচেতন প্রেরণাই কাজ করে।
পাঁচ কোটি হিন্দুস্তানী মুসলমানের স্বস্তি, সম্মান ও জীবন-জীবিকার বিনিময়ে অর্জিত পাকিস্তানে সমস্বার্থে ও সমমর্যাদায় যদি সহ-অবস্থান মুসলমানের পক্ষেই সম্ভব না হয়, তা হলে কাদের হিতার্থে এ পাকিস্তান!
অতএব, যে অর্থনৈতিক কারণে হিন্দুবিদ্বেষ জেগেছিল এবং ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতিগত স্বাতন্ত্রের জিকির তুলে আর্থিক সুবিধার জন্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত; আজ আবার সেই অর্থনৈতিক কারণে অর্থাৎ শোষণের ফলেই বাঙালি স্থানিক, ভাষিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্রের ভিত্তিতে স্বাধীনতা কিংবা অর্ধ-স্বাধীনতা দাবি করবে এই তো স্বাভাবিক। অন্তত ইতিহাস তো তা ই বলে।
একটি প্রতারক প্রত্যয়
ইসলাম সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং উন্মেষ যুগে তা আক্ষরিকভাবে অনুসৃতির প্রয়াস ছিল। তবু স্বার্থের ব্যাপারে সে-শিক্ষা ও সৌজন্য অবহেলিত হয়েছে বারবার। এতে একটি সত্য প্রতিষ্ঠা পায় : লোভের ও লাভের ক্ষেত্রেই হয় আদর্শের পরীক্ষা, আর লিপ্সার সঙ্গে দ্বন্দ্বে এবং স্বার্থের সংগ্রামে আদর্শ সাধারণত হার মানে। লোভ ও লাভ-চেতনা চিরকালই প্রবল এবং সে কারণেই বাস্তব। আদর্শবাদ ও নীতিবোধ সুন্দর বটে, কিন্তু সহজলভ্য নয়। বোধগত আদর্শ আবেগগত না হলে জীবনে আচরণ-সাধ্য হয়ে উঠে না। ইসলামী সাম্য এবং ভ্রাতৃত্বও তাই বৈষয়িক ও রাষ্ট্রিক ব্যাপারে কার্যকর হয়নি। এর কার্যকর হয়তো অসম্ভব ছিল না, কিন্তু বাস্তব জীবনে তা অস্বাভাবিকই প্রমাণিত হয়েছে।
যেমন, রসুলের ওফাত-মুহূর্তেই নেতৃত্বের দাবিতে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় আনসারে-মোহাজেরে। অবশেষে রসুলের স্বজনের দাবীই স্বীকৃতি পায়। প্রথম চার খলিফার চার জনই মক্কী এবং যথাক্রমে রসুলের দুই শ্বশুর ও দুই জামাতা। পরবর্তীকালে খিলাফতে আব্বাসীয় প্রতিষ্ঠাও আসে রসুলের জ্ঞাতিত্বের দাবিতে। তাছাড়া হযরত উসমানের পতনের কারণ ও হযরত আলীর প্রতিষ্ঠার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় মুখ্যত গোত্র-দ্বেষণা। এ দ্বেষ-দ্বন্দ্ব ও বিরোধ-বিবাদ ইসলাম-সংপৃক্ত মুসলিম ইতিহাসকে ম্লান করেছে।
হাশেমী-উম্মাইয়ার এ জ্ঞাতি-বিদ্বেষ আব্বাসীয়দের পতনকাল অবধি তীব্র ছিল। এবং তা কেবল উক্ত দুই বংশে সীমিত ছিল না। রসুলের স্বজন ও আত্মীয় হিসেবে হাশেমীরা পায় বিশ্ব মুসলিমের সহানুভূতি ও আনুগত্য। আর চিরঘৃণ্য হয়ে থাকে উম্মাইয়ারা। এ সহানুভূতি বশেই কারবালার যুদ্ধে নিহত হোসেন মুসলিম জগতে প্রিয়তম হয়ে উঠেন এবং কারবালা পায় তীর্থের মর্যাদা।
যদিও ইসলামী শাস্ত্রকে সুসংবদ্ধকরণ, ইসলামী সমাজকে পূর্ণাবয়ব দান, মুসলিম সাম্রাজ্যের কলেবর বৃদ্ধি প্রভৃতি প্রায় সবকিছু উম্মাইয়াদেরই কৃতি এবং কীর্তি, আর হাশেমীদের দান প্রায় দুর্লক্ষ্য, তবু রসুলের আত্মীয় হিসেবে শ্রদ্ধেয়তার সুযোগে মুসলিম জগতে তারা উম্মাইয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-বিষ ছড়িয়ে ছড়িয়ে জনমনে উম্মাইয়াদের প্রতি গভীর ঘৃণার সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল, যা চিরকাল দুরপনেয় হয়ে থাকবে। এ কারণেই ইসলাম ও মুসলিম সমাজের প্রতি উসমান-মালেক-উমর-ইয়াজিদ প্রমুখ কীর্তিমান শাসকদের অবদানও প্রায় অস্বীকৃত। এজন্যেই দেখতে পাই, সমাজে শ্রদ্ধেয়তা অর্জনের জন্যে যেমন হাশেমী কুলবাচি গ্রহণে মুসলিম সমাজে আগ্রহের আজো অভাব নেই, তেমনি মুসলিম সমাজের ঘৃণা এড়ানোর জন্যে আসল উম্মাইয়ারাও কুলবাচি পরিহার করে সমাজে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছিল।
অন্য ক্ষেত্রেও সাম্য, সমদর্শিতা ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ অনুসৃত হয়নি। সাম্রাজ্যিক স্বার্থে উমর আরবদের পক্ষে বিজিত আজমে বসবাস ও বিবাহ নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তেমনি ইরানী মায়ের সন্তান বলেই আল-মামুন সিংহাসনে বঞ্চিত হন। এবং মাতৃকুলের সাহায্যে বাহুবল প্রয়োগে তাকে দখল করতে হয় খিলাফৎ। আবার তা আয়ত্তে রাখার জন্যেও ফাতেমীদের তোয়াজ করতে হয় তাঁকে। এমনি দৃষ্টান্ত ছড়িয়ে রয়েছে ইসলামের ও মুসলমানদের ইতিহাসের সর্বত্র। বৈষয়িক ও রাজনৈতিক জীবনে সাম্য, সহযোগিতা কিংবা সহ-অবস্থানের দৃষ্টান্ত মুসলিম ইতিহাসেও গোড়া থেকেই বিরল। এক্ষেত্রে ইসলাম গোত্ৰ-চেতনা যেমন বিলোপ করতে পারেনি, তেমনি স্বধর্ম ভিত্তিক রাষ্ট্রিক জাতীয়তাও গড়ে উঠেনি কখনো। যদি তাই সম্ভব হত; তাহলে খলিফা বা আমীরুল মুমেনীনের কর্তৃত্বে দুনিয়ায় সব সময় একটি মাত্র মুসলিম রাষ্ট্র থাকত।
আজো আরবেরা ধর্মভিত্তিক জাতীয়তায় আস্থাবান নয়–গৌত্রিক কিংবা ভাষিক অভিন্নতা ভিত্তিক জাতীয়তার সাধক। ইরানীরা আর্য-চেতনাতেই সংহত। তাই দেশের নাম ইরান এবং শাসক আর্যমিহির ও পহলবী। পাক-ভারতের ইতিহাসে আফগান-তুকী-মুঘলের দ্বন্দ্ব ও বিরোধ আকস্মিক ও নয়, একদিনেরও নয়। অতএব ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রিক জাতীয়তা মুসলিম-ইতিহাসেও অনুপস্থিত।
পাক-ভারতে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত হল ইংরেজ আমলে ও প্রতীচ্য প্রভাবে। ইংরেজ আমলেই নেপাল থেকে সিংহল এবং বার্মা থেকে খাইবারপাস অবধি ভূ-ভাগ ব্রিটিশের একচ্ছত্র শাসনে আসে। বিদেশী শাসকের একচ্ছত্র শাসন ও শোষণ এবং যন্ত্রণার সমানুভূতি এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের শাসিত জনদেরকে ঐক্য দান করে। ইতিপূর্বে এত বড় মহাদেশ কখনো এক-কেন্দ্রিক শাসনে ছিল না। এর নতুন নাম হল ভারত সাম্রাজ্য।
উৎপীড়িত শাসিত জনেরা একক জাতি রূপে সংহত হয়ে স্বাধীনতা অর্জনে হল উৎসুক। কিন্তু অসংখ্য গোত্রে, নানা ধর্মে, বহু ভাষায় ও বিভিন্ন আঞ্চলিক পরিবেশে বিভক্ত এখানকার মানুষেরা সম সংখ্যার ও সম স্বার্থের অভাবে একই মিলন ময়দানে দাঁড়াতে পারল না। অসম সংখ্যা ও বিষম স্বার্থ সংহতি ও সংগ্রামের অন্তরায় সৃষ্টি করল। জাতীয় কংগ্রেস পরিণামে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর সংগ্রাম-সংস্থার রূপ নিল। সাম্রাজ্যভুক্ত মুসলমানরাও স্বাধর্মের আশ্রয়ে সংগ্রামী শক্তি অর্জনে হল তৎপর। ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমানদের এ সংগ্রাম ছিল প্রত্যক্ষত ধন-মানের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুর বিরুদ্ধে। স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে এর শুরু আর উনিশশ সাতচল্লিশে এর সমাপ্তি।
আমাদের এ ধারণার সমর্থনে প্রবল প্রমাণ উপস্থিত করতে পারি। পলাশীর যুদ্ধে বিদেশী খ্রস্টানদের হাতে বাঙলার সুবাদারের পরাজয় ভারতের কোনো রাজন্যকেই বিচলিত ও বিব্রত করেনি। তারও প্রায় দুশ বছর আগে বিদেশী বিধর্মী বেনেরা গোয়া-দামন-দিউ-কারিকল-মাহে দখল করেছিল। কিন্তু কোনো দেশী রাজন্যের আত্মসম্মানে তা আঘাত করেনি। তারা বরং ওদেরকেও কাড়াকাড়ি আর শাসন-শোষণের খেলায় নবাগত প্রতিযোগীরূপেই গ্রহণ করেছিল। খেলোয়াড়-সুলভ প্রতিযোগিতা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা অবশ্য ছিল। কিন্তু বিদেশী-বিধর্মী-বিজাতি বলে ঘৃণা-বিদ্বেষ ছিল না। কেননা, শাসক বা শাসিত জনের মধ্যে স্বাদেশিক কিংবা স্বাজাতিক চেতনা ছিল অজাতমূল। তাই পলাশীর যুদ্ধের পরেও একশ বছর ধরে গোটা ভারত গ্রাসকালে স্বাজাতিক বা স্বাদেশিক প্রেরণা বশে ব্রিটিশকে বাধা দেবার চিন্তাও করেনি কেউ। সিপাহী বিদ্রোহের সুযোগও তাই নিতে চায়নি অনুগত ও অনুরক্ত রাজন্য কিংবা ইংরেজি শিক্ষিত সৃজ্যমান ধনী ও মানী সমাজ।
অতএব দৈশিক জাতীয়তাবোধ পাশ্চাত্যশিক্ষার দান। এই শিক্ষার মাধ্যমে দেশী লোকের মনে ক্রমে যে আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত হয়, যে-জীবন-চেতনার উদয় ঘটে, তারই ফলে বিশ শতকের গোড়া থেকে স্বাধীনতার স্পৃহা ঘনীভূত হতে থাকে। এ স্পৃহা যে কেবল ব্রিটিশ ভারতেই জেগে ছিল তা নয়, বিশ শতকের উষাকাল থেকে গোটা দুনিয়ার শাসিত-শোষিত জনেরা দৈশিক জাতীয়তার মাধ্যমে মুক্তি ও সংগ্রামের সংকল্প গ্রহণ করেছিল। এই দৈশিক জাতীয়তার প্রেরণায় আরব মুসলিমরাও তুর্কী খলিফার আনুগত্য ও শাসন অস্বীকার করেছিল। অতএব স্বাধৰ্ম সংহতির সহায়ক নয়। আসলে ঐক্যের ভিত্তি হচ্ছে সমস্বার্থ। এবং এই স্বার্থ সবক্ষেত্রেই ভৌগোলিক অবস্থানগত। পৃথিবীর সর্বত্র তাই আজ আঞ্চলিক ফলত ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধ ও রাষ্ট্রচিন্তা প্রিয় ও প্রবল।
ব্রিটিশ ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানরাও–স্বাধ বশে নয়, সম-স্বার্থেই সংহত হয়েছিল সংখ্যাগুরু হিন্দুর প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে। সুযোগ ও সম্পদের নিরাপত্তা-বাঞ্ছই তাদেরকে সংহতি দিয়েছিল। ব্রিটিশ ভারতে এই অভিন্ন লক্ষ্যে নিয়োজিত তাদের সঙ্- শক্তি ফলপ্রসূ হয়েছিল। লক্ষ্য বা গন্তব্যের অভিন্নতা যে-সাহচর্য ও সহযোগিতার আবেগ ও আগ্রহ জাগিয়েছিল, গন্তব্যে উত্তরণের পর তাতে স্বভাবতই শৈথিল্য এল। এর কারণ দুটো। এক. সাফল্যে প্রয়াসের প্রেরণা এখন অপগত। দুই. আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতা ও ভাষিক বিভিন্নতার দরুন সমস্বার্থের সমতল ভূমি এখন দুষ্প্রাপ্য।… কাজেই বন্ধনসূত্র এখন শিথিলগ্রন্থি। বৈষয়িক স্বার্থের যে-মানস-প্রেরণা সংহতি দিয়েছিল, দৃশ্যত তার বাহ্যিক আবরণ ছিল স্বাধর্ম। যদিও তা ত্রাণের বর্মরূপে ক্রিয়া করেনি, তবু বক্তব্যের আবরণ রূপে কেজো ছিল।
আমাদের এ ধারণার সমর্থনে সাক্ষ্যও রয়েছে। ইংরেজি শিক্ষা ও বিধর্মী-বিরল তখনকার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অর্থাৎ এখনকার পশ্চিম পকিস্তানে মুসলিম লীগের প্রচারণা সত্ত্বেও মুসলিম জাতীয়তার আহবানে সাড়া মেলেনি। এ আবেদন বিপুল বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চলের শোষিত মুসলিম সমাজে ও চাকুরি-বঞ্চিত শিক্ষিত মুসলিম মনে। কাজেই স্বাধর্মের অঙ্গীকার জাতীয়তার প্রতিজ্ঞায় প্রত্যয় ছিল না ব্রিটিশ ভারতের সর্বাঞ্চলের মুসলিম মনে। সুতরাং স্বাধর্মভিত্তিক জাতীয়তার নজির মেলে না ইতিহাসে।
অতএব রাষ্ট্রিক প্রয়োজনে মিলনের অন্য ময়দান খুঁজতে হবে। ইসলামের দোহাইতেও যখন আত্মীয়তা গড়ে উঠছে না, তখন ঐক্যের সূত্ৰ সন্ধান করতে হবে অন্যত্র ও অন্যভাবে। সুযোগ ও সম্পদের ক্ষেত্রে সুবিচার ও সমদর্শিতার অঙ্গীকারে অবশ্য মিলন স্থায়ী ও স্বস্তিকর করা সম্ভব। প্রীতিপ্রসূত পারস্পরিক বিশ্বাস ও ভরসাই কেবল মিলন-রাখী অটুট রাখতে পারে। নইলে মিশর সিরিয়ার মিলনের মতো তা নশ্বর হতে বাধ্য। আজকের আরব রাষ্ট্রগুলো যেমন স্বতন্ত্র থেকেও স্ব স্ব স্বার্থে অভিন্ন শত্রু ইসরাইলকে ঘায়েল করবার জন্যে আরব জাতীয়তার নামে ও আবেগে ঐক্য ও সংহতি কামনা করছে, ব্রিটিশ ভারতেও স্ব স্ব আঞ্চলিক স্বার্থে মুসলিমরা স্বাধর্মের নামে আবেগ সঞ্চয় করে সঙ্বদ্ধ হতে চেয়েছিল আপাত উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই।
তাছাড়া ধর্মীয় জাতীয়তার পথে একটি গুরুতর সমস্যও রয়েছে। এক ধর্মের লোক কেবল এক অঞ্চলে বাস করে না, সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করে। কাজেই স্বধর্মীকে নিয়ে যদি জাতি-চেতনা লালন করতে হয়, তাহলে রাষ্ট্রিক জাতীয়তা জন্মাতে পারবে না, অথচ এটি এ-যুগে রাষ্ট্রিক স্বার্থে জরুরী। তাছাড়া দুনিয়ার কোনো দেশেই কেবল এক ধর্মাবলম্বী বা এক মতাবলম্বী মানুষ বাস করে না। নানা জাত-মত ও বর্ণ-ধর্মের মানুষ নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রে সংখ্যাগুরু ধর্মীয় জাতীয়তাই যদি রাষ্ট্রিক জাতীয়তার নামান্তর হয়, তাহলে রাষ্ট্রে বিধর্মীরা স্বাধীনতার স্বস্তি বা গৌরব বোধ করে না। তখন তারা সংখ্যাগুরুর পাশে থেকেও পড়শী হয় না। জাতীয় কিংবা সাংস্কৃতিক ও রাষ্ট্রিক ঐতিহ্যে অনধিকার তাদেরকে প্রবাসীর মতো পর ও আশ্রিতের মতো অসহায় অনুগ্রহজীবী করে রাখে।
ফলে বাইরে তাদেরকে রাষ্ট্রানুগত দেখায় বটে, কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক কারণেই অন্তরে থাকে বিরূপতা, এবং রাষ্ট্রের সঙ্কটকালে তা সমস্যা হয়ে দেখা দেয়। পোল্যান্ড ও রাশিয়ার ইহুদী বিতাড়ন এবং প্রথম মহাযুদ্ধকালে জার্মান-ইহুদীর ভূমিকা এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে জার্মানিতে ইহুদী-নিধন এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। এ যুগে জাতীয়তা দেশগত না হলে রাষ্ট্রিক জীবনে স্বস্তিকর হয় না।
এক্ষেত্রেও পূর্ব বাঙলার সমস্যা ও দুর্ভাগ্য বিবেচ্য। মুসলমানের পক্ষে ইসলামী শাসনতন্ত্র ও রাষ্ট্রব্যবস্থার মতো কাম্য বিষয়েও নিহিত রয়েছে বাঙালি মুসলিমের অস্বস্তির ও অমঙ্গলের বীজ। এখানে অমুসলিম প্রতিবেশী নিয়ে ঘর করি আমরা। ইসলামী বিধি ও রাষ্ট্ৰাদর্শের অঙ্গীকারে যে নাগরিকত্বে আমাদের উল্লাস, তাতে তারা মনে মনে বঞ্চিতের বেদনা ও অপমানিতের ক্ষোভ অনুভব করে। এভাবে আমরা ঘরের মানুষকে পর ও বিরূপ করে তাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছার ফসল থেকেই যে কেবল নিজেদেরকে বঞ্চিত করছি, তা নয়, আমাদের স্বস্তি-সুখও বিঘ্নিত ও বিপন্ন। থাকছে। মাঝে-মধ্যে বিধর্মী-হত্যা–যার ভদ্র নাম দাঙ্গা, এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অতঃপর দেশপ্রাণতায় ও রাষ্ট্রানুগত্যে কী হবে তাদের প্রেরণার উৎস ও অবলম্বন? জিম্মি-জীবনের গ্লানি ঘুচবে কোন্ অনায়াসলভ্য চিত্ত-সম্পদের ঐশ্বর্যে? বিধর্মীবিরল পশ্চিম পাকিস্তানে এ সমস্যা অনুপস্থিত। তবে কী ইসলামী শাসনতন্ত্র ও রাষ্ট্রাদর্শ গ্রহণের মতো মহৎ অভিপ্রায়ের মধ্যেও ভেদনীতির প্রশ্রয়ে পূর্ব বাঙলায় স্থায়ী শাসন ও কায়েমী শোষণের অভিসন্ধি নিহিত!
পূর্বকালের রাজ্যে এ সমস্যা ছিল না। কেননা তখন রাজ্য ছিল রাজার, প্রজা ছিল শাসন শোষণের ও কৃপা-পীড়নের পাত্র। রাজ্য ছিল রাজার আয়ের ও আরামের জমিদারী। রাজস্বের জন্যেই তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল রাজ্যের নিরাপত্তা বিধান ও প্রজারক্ষণ। কেননা সুখ-সৌভাগ্যে যেমন থাকত তার একাধিকপত্য, তেমনি দুঃখ-দুর্ভাগ্যও তাঁকেই বহন করতে হত। আজ মানবাধিকারের সীমা দূরবিস্তৃত। তাই আজ মানুষ আর প্রজা নয়–পৌরজন। এ যুগে দেশগত বা রাষ্ট্রগত জাতীয়তা জরুরী নয় কেবল, রাষ্ট্রের ভিত্তিও। অতএব ধর্মীয় জাতীয়তা একটি আত্মধ্বংসী প্রতারক প্রত্যয়।
একটি বীজমন্ত্রের তাৎপর্য
০১.
ধর্মকে ধারণ করেই মানুষ ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে নির্ঘ ও নির্বিঘ্ন জীবনযাত্রার পথ করে নিতে চায়। অবশ্য এ ব্যাপারে সে কোনো স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য কামনা করে না। সে জন্মসূত্রে তার ঘরোয়া ও সামাজিক পরিবেশ থেকে যা পায়, তা-ই সে নির্বিচারে গ্রহণ করে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করবার চেষ্টা করে। আশৈশব লালিত সংস্কারই তার এ বিশ্বাসের ভিত্তি। এবং তার জীবন ও জগৎ চেতনাও অনেকাংশে এই বিশ্বাস-সংস্কার প্রসূত। ধর্মের ক্ষেত্রে মানুষ কৃচিৎ জ্বিজ্ঞাসু–এর জন্যে কিছুটা ব্যক্তিগত ঔদাসীন্য আর অনেকটা সামাজিক অসহিষ্ণুতা ও শাস্ত্রীয় নিষেধই দায়ী। এই অসহিষ্ণুতা ও নিষেধের গোড়ায় রয়েছে জীবনের পথ ও পাথের সম্পর্কে নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত হবার আগ্রহ। এ কারণেই কোন-না-কোনো জ্ঞানী-মনীষী প্রদত্ত দিশার অনুসরণে সে নিশ্চিন্ত নির্বিঘ্ন জীবন-দর্শন গ্রহণে অভিলাষী। তাই মানুষ সাধারণভাবে পরবুদ্ধিজীবী।
কিন্তু ধর্ম বলতে কোনো অবিমিশ্র একক মত বা শাস্ত্র বুঝায় না। আদিম আরণ্য মানবের আঞ্চলিক জীবন ও জীবিকা পদ্ধতির প্রভাবে গড়ে উঠেছিল যে জীবন-চেতনা ও জগৎ-ভাবনা, তাই প্রতিবেশিক ও জৈবিক প্রয়োজনে ক্রমবিকাশের ও ক্রমবিবর্তনের ধারায় কালিক রূপান্তর লাভ করেছে। মানব-চেতনার বিকাশ ও ব্যবহারিক প্রয়োজনের প্রসারই তার সর্বাত্মক ও সর্বাঙ্গীণ বৃদ্ধি ও ঋদ্ধির মূলে ক্রিয়াশীল। এ কারণে এর উপর স্থানগত ও কালগত জীবিকা-পদ্ধতির প্রভাব অপরিমেয়। তাই ধর্মের স্থানিক ও কালিক অবয়ব ও বিকাশ ছিল–দেশ-কাল নিরপেক্ষ রূপ ছিল না। এমনকি এর মধ্যে প্রকৌশল, অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনবোধের প্রভাব এত অধিক ছিল বলেই আরণ্য মানবের ধর্মে আর সভ্য ও সভ্যতার মানুষের শাস্ত্রে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও প্রয়োজনগত পার্থক্য এবং মনন ও রুচির উৎকর্ষ ও অপকর্ষ সর্বক্ষেত্রে সুপ্রকট।
অতএব, ধর্ম বলতে ঈশ্বর, ভূত-প্রেত, জীন-যাদু, সুখ-দুঃখ, রোগ-শোক এবং স্বর্গ-মর্ত পাতাল সমন্বিত এক বিরাট-বিপুল চির রহস্যাবৃত মায়াময় কল্পনোক বা মানস-জগৎ বোঝায়–যার জটিল আলো-আঁধারীর মধ্যে রয়েছে–আমাদের বাস্তব জীবনের সম্পদ ও সমস্যার, আনন্দ ও যন্ত্রণার, স্বপ্ন ও সত্যের রহস্যসূত্র। অজ্ঞ অসহায় মানুষ অনুমানে ও অনুভবে এই রহস্যভেদে ছিল প্রয়াসী। যা বুঝেছে তার ভিত্তিতেই সে জীবনের ও জীবিকার সেই অদৃশ্য অরি ও মিত্র শক্তিগুলোর সঙ্গে একটা আপোষ-রফা করবার চেষ্টা করেছে পূজা-পার্বণ ও আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এর জন্যেই প্রয়োজনীয় হয়েছে নিয়ম-নীতি। যৌথ জীবনের অবচেতন প্রেরণায় ও প্রয়োজনে সে চুক্তিতে এসেছে মানুষেরও সামাজিক ও বৈষয়িক জীবনের নিয়ম-নীতির শৃঙ্খল। তাই এ চুক্তি ত্রিপক্ষীয়–দেব, দানব ও মানুষের পারস্পরিক অধিকার, দাযিত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত হয়েছে মানুষের ব্যক্তিক আনুগত্যের অঙ্গীকারে দেবতা-দানবের অনুগ্রহ, সহযোগিতা ও সহিষ্ণুতার ভিত্তিতে।
এখানেই কিন্তু মানুষ থামেনি। নিশ্চিন্ত হতে পারেনি এ ব্যবস্থায়। তার প্রসারমাণ জীবনের প্রয়োজনে সে নৈতিক, সামাজিক, বৈষয়িক ও প্রশাসনিক নিয়ম-নীতির মধ্যে নিজকে নিবদ্ধ করে যৌথ জীবনের নিরাপত্তা ও শান্তি কামনা করেছে। এমনি করে মানুষ এক বিপুল ও বিচিত্র জীবন যন্ত্র এবং জটিল-জীবিকা যান তৈরি করে এগিয়ে এসেছে আজকের দিনে। আজ ধার্মিক, নৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক নিয়মকানুনের নিগড়ে মানুষ স্বেচ্ছাবন্দী। এ বন্দিত্ব বরণ করেছে সে শান্তি, স্বস্তি, প্রগতি ও কল্যাণ আকাঙ্ক্ষায়। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ও প্রকৌশলে মানুষের বিস্ময়কর অগ্রগতি পৃথিবীকে করেছে সংহত এবং মানুষের সমাজ করেছে সংমিশ্রিত।
আত্মপ্রত্যয়ী যন্ত্রী মানুষ আজ আর কোনো ব্যাপারেই দৈব-নির্ভর নয়। দেব-দানবের সঙ্গে তার চুক্তি ভেঙে গেছে। জীবনের কোনো প্রয়োজনের জন্যে সে আর আসমানের অনুগ্রহ-প্রত্যাশী নয়। মানতেই হবে, যারা মানব-শক্তির এমনি অচিন্ত্য বিকাশ সাধন করেছেন, তাঁরা চিত্ত-সম্পদে অতুল্য। এদের সাধনা ও শ্রমের, এদের ভাব, চিন্তা ও কর্মের দান যে যন্ত্রজ বস্তু-সম্পদ–তা অকাতরে দ্বিধাহীনচিত্তে পরম আগ্রহে গ্রহণ করেছে কর্তব্যে উদাসীন, পরচিন্তাজীবী ও পরশ্রমজীবী ভোগেছু মানুষ। কিন্তু মানুষ নির্বোধের মতো পরিহার করে চলে তাদের চিত্ত-সম্পদ, অবজ্ঞা করে তাদের মননের মহাঅবদানকে। ব্যবহারিক-বৈষয়িক জীবনে তারা বরণ করেছে বাস্তব জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যকে, চলমানতাকে; কিন্তু মানস-জীবনে গ্রহণ করেনি এই যান্ত্রিক বস্তুর জনন-শক্তিকে, সেখানে তারা ধরে রেখেছে স্থিতিশীলতাকে। জীবন-ভাবনায় ও জগৎ- চেতনায় মানুষের এই অসঙ্গতি, বস্তু-সম্পদে এই আগ্রহ এবং চিত্ত-সম্পদ অর্জনে এই অনীহাই আজকের দিনের সব চাইতে মৌলিক মানবসমস্যা। এ সমস্যার সমাধান হলে, আমাদের বিশ্বাস অন্য সব মানবিক সমস্যার সমাধান হবে অনায়াসলভ্য।
.
০২.
আমাদের পাকিস্তানে এই সমস্যা আরো বিকৃত হয়ে দেখা দিয়েছে। সে কথা এখন বলব।
ধর্ম-বিরহী দেশ নেই। এবং শাস্ত্রীয় ধর্ম ও আচারিক, আনুষ্ঠানিক আর পার্বণিক ধর্ম মানুষের আটপৌরে জীবনে চেতন-অচেতনভাবে জড়িয়ে রয়েছে! এতকালের পুরোনো ধর্ম মানুষের ব্যবহারিক-বৈষয়িক জীবনে কোনো সহায়তাও করে না, স্বস্তি-শান্তির বিঘ্ন ঘটায় না। এ একরকম গৌরব-গর্বের ও প্রবোধ-প্রশান্তির অবলম্বন হয়েই আভরণের মতো জীবনে সংলগ্ন।
কিন্তু পাকিস্তানের সরকার, সরকারি লোক ও জননেতার কাছে ধর্ম একটি তরতাজা প্রাত্যহিক ও বৈষয়িক সম্পদ ও সমস্যা। তাঁরা যেন ইসলাম ও মুসলমানের প্রাচীনত্ব–সাড়ে তেরোশ বছর বয়স–স্বীকার করতে চান না। উন্মেষ যুগের সাহাবী-প্রচারকদের মতো তারা যেন সদ্যোজাত ইসলাম প্রচারে এবং নও-মুসলিম রক্ষণে সদাবিব্রত। তাঁদের চোখে ইসলাম ও মুসলমানের ভয়ঙ্কর সঙ্কটজনক অবস্থা। উভয়েরই যেন এখন-তখন হাল। কখনো ইসলাম ডোবে, কখনো মুসলমান মরে, আবার কখনো বা সিরাজুল ইসলাম নিবে!
তাদের ঘরোয়া জীবনে ইসলামের প্রতি ঔদাসীন্য সাধারণ লোকের চাইতে বেশি বলেই শোনা যায়। কিন্তু তাঁদের দফতর ও ময়দানী-জীবনে তারা ইসলামের সমর্পিত চিত্ত, ইসলাম-সর্বস্ব ও ইসলামের জন্যে উৎসর্গিতপ্রাণ। তাই তারা ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামী জীবন-পদ্ধতি, ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠাকামী। তাঁদের অভিপ্রায় অতি উত্তম এবং আপাত দৃষ্টিতে সবটাই ভালো।
কিন্তু তাঁদের উৎসাহের আতিশয্য দেখে মনে হয় পৃথিবীর আর কোথাও ইসলাম ও মুসলিম নেই। কেবল পাকিস্তানেই বিপন্ন ইসলাম ও মুমূর্ষ মুসলমান শিবরাত্রির সলতের মতো সধূম শিখা নিয়ে টিকে রয়েছে এবং তাও নির্বাণোন্মুখ। তাই জননেতা ও সরকারের এই বিচলন এবং তজ্জাত উদ্বেগ ও উত্তেজনা। অছির দায়িত্ব চিরকালই গুরু ও মহৎ দায়িত্ব। সে দায়িত্বে অবহেলা অসম্ভব!
.
০৩.
এবার পাকিস্তানীর হালফিল অবস্থা বিবেচনা করা যাক। পশ্চিম পাকিস্তানে প্রায় সবাই এবং পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা নব্বই জন অধিবাসীই মুসলমান। সরকার ও জননেতারা বলেন ইসলাম ও ইসলামী জীবনযাত্রার প্রতি আকর্ষণ বশেই তারা পাকিস্তান তথা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র কামনা করেছিলেন। এর মধ্যে তথ্যের ভুল যা-ই থাক, তাদের অভিপ্রায়ের অকৃত্রিমতায় আস্থা রাখতে আমাদের আপত্তি নেই।
বিগত কয় বছর ধরে পাকিস্তানও ইসলামী রাষ্ট্র। এবং ঘরে-বাইরে তা সগৌরবে ও সগর্বে প্রচারও করা হয়। পাকিস্তানী মুসলমানদের সবাই শাস্ত্রে সুপণ্ডিত না হোক, প্রাত্যহিক জীবনে -আচরণীয় ও অবশ্য পালনীয় শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ সম্পর্কে শিক্ষিত, অশিক্ষিত কিংবা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে অবহিত। অন্তত শাস্ত্রীয় পাপ-পুণ্য ও ন্যায়-অন্যায় সম্পর্কে কেউই অজ্ঞ নয়।
তবু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর যুগে স্বাধীনতা-প্রাপ্ত আফ্রো-এশিয়ার অনুন্নত কিংবা উন্নয়নশীল অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় ইসলামী রাষ্ট্র পাকিস্তানে, কোন্ পাপ কোন্ অন্যায় কম! ওরা অবশ্য পাকিস্তানীদের মতো অত ধর্মভীরু বা ধর্মপ্রিয় নয়, তাদের রাষ্ট্রও ধর্মরাষ্ট্র নয়। তবু সততায়, ন্যায়পরায়ণতায়, কর্মনিষ্ঠায়, দায়িত্বশীলতায় কিংবা কর্তব্যবুদ্ধিতে ধর্মে অনুরক্ত ও অনুগত ইসলাম সর্বস্ব পাকিস্তানীদেরকে ঘরে-বাইরে কোথাও আমরা বিজাতি-বিধর্মীদের চেয়ে ভালো দেখিনে। ঘরোয়া জীবনে, সামাজিক অঙ্গনে, অফিসে-আদালতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে-মিথ্যার বেসাতি, অন্যায়ের নির্লজ্জ প্রকাশ, বিবেকের অবমাননা সর্বত্র দৃশ্যমান। দ্বেষ-দ্বন্দ্ব-সংগ্রাম ও পীড়ন-লুণ্ঠন হনন প্রভৃতি নিত্যকার ঘটনা। চোরাকারবারী, কালোবাজারী, চুরি, ডাকাতি, কর্তব্যে অবহেলা, অন্যায়-প্রবণতা, ঘুষ, ছল, প্রতারণা, মিথ্যাচার, জুয়া প্রভৃতি সর্বপ্রকার শাস্ত্রীয় পাপে পাকিস্তানীদেরকে যে-সংখ্যায় আসক্ত দেখি, তার চাইতে বেশি সংখ্যায় পাপে লিপ্ত ব্যক্তি অন্যদেশে আছে বলে আমাদের জানা নেই।
এ ব্যাপারে গণ-অভিভাবকদের মনোভাবও অদ্ভুত। এসব কিছুতেই যেন ইসলামের ক্ষতি হয় না, মুসলমানের জাত যায় না। কিংবা কোনো বিদেশী-বিজাতির আচারে-প্রভাবেই তাদের আপত্তি নেই–সর্বনাশ হয় কেবল ভারতীয় প্রভাবে ও হিন্দুয়ানী আচারে! আবার মুসলমান চোরা-ডাকু মিথ্যুক-লম্পট-বদমাশ হলে সমাজের কিংবা ইসলামের যেন কোনো ক্ষতি নেই,–ক্ষতি হয় কেবল কেউ নাস্তিক হলে। তারা আমাদের ভাত-কাপড়-ওষুধের দায়িত্ব নেন না, আমাদেরকে শুধু ভেহেস্তে পাঠানোর কর্তব্য পালনেই তাদের আগ্রহ। আর তাও সর্বত্র এবং সর্বদা নয়–কেবল দফতরে ও ময়দানে এবং সরকারি সমস্যার কালে ও নির্বাচন সময়ে।
তাহলে এই আদর্শিক ইসলাম-প্রীতির রহস্য অন্যত্র সন্ধান করতে হবে।
প্রথমত, ধরা যাক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে কী কী পাপ ও অনাচার থাকে, যা ধর্ম-রাজ্যে চালু নেই। বলতেই হবে তেমন পার্থক্য নির্দেশ করা দুঃসাধ্য। ইসলামে নিষিদ্ধ বা ধিকৃত সিনেমা, জুয়া, ঘোড়দৌড়, সঙ্গীত, সুদ, নারী-স্বাধীনতা, বেশ্যাবৃত্তি, মাদকদ্রব্য, বীমা প্রভৃতি পাকিস্তানেও চালু রয়েছে। তবে ইসলামী শাসনতন্ত্রের বা সরকারের বৈশিষ্ট্য কি?
দ্বিতীয়ত, ইসলামী শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হলেই মুসলমান চরিত্রবান হবে, ধার্মিক হবে এমন ধারণার স্বপক্ষে যুক্তিও প্রবল নয়। চুরি, ঘুষ, সুদ, মিথ্যাচার, পীড়ন প্রভৃতি সম্বন্ধে সামাজিক পাপবোধ জাগানোর জন্যে কোনো বিশেষ শাস্ত্রীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করা দুঃসাধ্য। কেননা দুনিয়ার কোনো সভ্য-অসভ্য, আস্তিক-নাস্তিক সমাজেই এসব দুষ্কর্মের সমর্থন নেই। তাছাড়া বিদ্যা বা শিক্ষা কিংবা জ্ঞান মানুষের চরিত্র গড়ে না। বৃত্তি-প্রবৃত্তি সংযত রাখার সদিচ্ছাই ব্যষ্টিকে চরিত্রবান, নীতিনিষ্ঠ ও আদর্শপরায়ন করে। বিদ্বান বা জ্ঞানী হলেই চরিত্রবান হবে–এমন কথা শাস্ত্রীয় তত্ত্ব হলেও সামাজিক তথ্য নয়। তার প্রমাণ আমাদের শিক্ষিত লোকের মধ্যে চরিত্রহীনের সংখ্যা যত বেশি, অশিক্ষিত সমাজে তত নেই।
আমাদের দুর্নীতির সমস্যা তো শিক্ষিত ব্যবসায়ী ও চাকুরিজীবী সমাজেই সীমিত। বরং নিরক্ষর লোকেরা আজন্মলালিত ঘরোয়া বিশ্বাস-সংস্কারের প্রভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে বলেই বিশেষভাবে দৈবনির্ভর ও নিয়তি-ভীরু। জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে দৈব রোষ ও প্রসন্নতা-সচেতন বলেই তারা ভয়ে ভয়ে বাঁধা নিয়মে ও নীতিতে নিষ্ঠ থেকে জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে নির্বিঘ্ন ও নির্ঘ হতে প্রয়াসী। তাদের বিশ্বাসের ধর্ম তাদেরকে যান্ত্রিক-জীবন যাপনে উৎসাহ দেয়। এতে তাদের মানসক্ষেত্র বন্ধ্যা থাকে বলে চিত্ত-সম্পদ অর্জনের পথ রুদ্ধ থাকে বটে, কিন্তু সংস্কারলব্ধ ধর্মীয় ও সামাজিক নিয়ম-নীতির আনুগত্যে তাদের পতন-পথও থাকে বন্ধ। সুতরাং তাদের আত্মিক উৎকর্ষ-উন্নয়ন যেমন নেই, তেমনি অবনতিও নেই।
অতএব, চরিত্র গঠনের জন্যে শাস্ত্র-শিক্ষার যৌক্তিকতা সামান্য। আর রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, ভূতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, মৃৎবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজ-বিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভূগোল, বাণিজ্য, দর্শন, ইতিহাস, ভাষা প্রভৃতিতে ধর্মীয় শিক্ষানীতির সম্পর্ক ও সংলগ্নতা আবিষ্কার অসম্ভব। এসব জ্ঞানজ বিদ্যার সঙ্গে বিশ্বাসভিত্তিক শাস্ত্ৰনীতির কী সম্পর্ক রয়েছে যে শিক্ষানীতিও শাস্ত্রীয় হবে?
শাসনতন্ত্র ইসলামী করার সার্থকতাও দুর্লক্ষ্য। আমরা জানি, মুসলমান বা যে কোনো ধর্মাবলম্বীর শাস্ত্রীয় জীবন ও আচার সব সময়েই শাস্ত্রীয় আইনে নিয়ন্ত্রত হয়। এর জন্যে হিন্দু বা মুসলিম আইন রয়েছে। এর বাইরে বৈষয়িক জীবনে শাস্ত্র শাসন অনভিপ্রেত নয় কেবল, অকেজোও বটে। বাণিজ্য, দেশরক্ষা, যোগাযোগ, স্বরাষ্ট্র, শিক্ষা, অর্থ, উন্নয়ন, সেচ, কৃষি প্রভৃতি সরকারি দায়িত্বে ও কর্তব্যে শাস্ত্রীয় কী কাজ আছে যে শাসনতন্ত্র শাস্ত্রীয় হওয়া দরকার?
অতএব পাকিস্তানীদের সবক ও সরব ইসলাম প্রীতির অন্তরালে তিনটে কারণ অনুমান করা সম্ভব।
এক, অজ্ঞ জনসাধারণ যেহেতু চিত্তলোকে মধ্যযুগীয় জীবন-চেতনা লালন করে; সেজন্যে তাদের স্বাতন্ত্র, গৌরব-গর্ব, জীবন-ভাবনা ও জগৎ-চেতনা আজো স্বধর্মকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। তারা স্বধর্মের মাহাত্ম্য এবং স্বজাতির কৃতিত্বে ও সংখ্যাধিক্যে গৌরব-গর্বের আনন্দ ও কৃতাৰ্থমন্যতা লাভ করতে চায়। তাই তারা ইসলামী ও মুসলিম শাসনেই তুষ্ট। লাভ-ক্ষতির কথা তাদের মনে জাগে না।
দুই. মোহাজেরমাত্রেই নিরাপত্তার অবচেতন প্রেরণায় ইসলাম, ইসলামী শাসন ও ইসলামী জাতীয়তা-প্রবণ। কেননা বিদেশে বিভাষীর মধ্যে বসবাসের পক্ষে এটাই তাদের একমাত্র Locus Standi–স্বাধর্মের অধিকারেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের স্থিতি। এই ইসলাম ও মুসলিম প্রীতির পশ্চাতে অবশ্য বিধর্মীর নিষ্ঠুর পীড়নে ধন-জন-বাস্তু হারানোর ক্ষোভ আর বেদনাও সক্রিয়। আমাদের পরিচিত মোহাজেরদের প্রায় সবাই ইসলামী তথা মুসলিম জাতীয়তায় ও ইসলামী শাসনতন্ত্রে আস্থাবান।
তিন. অভিন্ন জাতীয়তার নামে সম্পূর্ণ ভিন্ন দেশের, গোত্রের, ভাষার, সংস্কৃতির ও জীবিকা পদ্ধতির মানুষকে এক রাষ্ট্রভুক্ত করে শাসন ও শোষণ করার জন্যে পশ্চিম পাকিস্তানীদেরও Locus standi হচ্ছে ইসলাম। কাজেই সে সুপরিকল্পিত সামাজিক নীতি অনুসৃতির ফলে বাঙালিকে তারা ভাষা বদলাও, হরফ বদলাও, বানান বদলাও, শব্দ বদলাও, পোশাক বদলাও, আচার বদলাও, দেশ ও দেশবাসীর নাম বদলাও বলে বলে উদ্বস্ত করেছিল; সেই নীতিরই আর এক চাল হচ্ছে ইসলামের জিকর, তথাকথিত ইসলামী শাসনতন্ত্রের মাহাত্ম্য ঘোষণা ও ইসলাম-ভিত্তিক মুসলিম জাতীয়তার অপরিহার্যতা বয়ান। শুনে শুনে শুধু গণ-মানব নয়, শিক্ষিতলোকও বিচলিত, বিব্রত ও বিগলিত। এতে বাঙালির দ্বিবিধ ক্ষতি : এক, এই ইসলামী বেরাদরীর মোেহবশে সে কখনো স্বস্থ ও স্বতন্ত্র হতে পারবে না। দুই. অমুসলিম-অধ্যুষিত এই পাক-ভূমে ইসলাম জোশ বিধর্মী-বিদ্বেষ জিইয়ে রাখবে।
আর নাগরিকত্বের সহজ অধিকারে বঞ্চিত বিধর্মীরাও স্বভূমে প্রবাসী হয়ে বাস করার লাঞ্ছনা ও গ্লানি এখনো মন থেকে মুছে ফেলতে পারবে না। তাদের মানস-বিরূপতা এ অঞ্চলের শান্তি, শক্তি ও প্রগতি বিঘ্নিত ও বিপন্ন রাখবে। রাষ্ট্রনীতিতে ইসলামী চেতনা, ইসলামী শাসনতন্ত্র, এবং ইসলামী জাতীয়তা প্রভৃতির মতো বাঙালির সংহতি বিনষ্টির এবং ভেদনীতি প্রয়োগের এমন মোক্ষম উপায় সম্প্রতি আর একটিও জানা নেই।
এ ছাড়াও অমুসলিমকে জিম্মিরূপে আলাদা করে রাখলে ভারতে তাদের জ্ঞাতি হত্যার প্রতিশোধ নেয়া যাবে, আবার বাঙলা থেকে হিন্দু উচ্ছেদ হলে বাঙালির সংখ্যাগরিষ্ঠতা নষ্ট হবে–এ দ্বিমুখী লাভের চিন্তাও যে তাদের প্রশ্রয় পায় না, তা নিঃসংশয়ে বলা যাবে না। তার উপর, বাঙালি মুসলিম মনে হিন্দু-বিদ্বেষ যে পরিমাণে তাজা ও প্রবল থাকবে, মুসলিম বেরাদরীভাবও সেই অনুপাতে ঠাঁই করে নেবে বাঙালি চিত্তে এমন একটা আশাও হয়তো উঁকি মারে মনের কোণে। এমনি করে নানা ছল-চাতুরীর মায়াজালে জড়িয়ে,নানা ছদ্মবাঁধনে অক্টোপাসের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে বাঙালি সত্তার ইতি সাধনে তৎপর রয়েছে কায়েমী স্বার্থবাদী বুর্জোয়া সাম্রাজ্যবাদীরা।
শাসন-শোষণের এমন যাদু-যন্ত্রের সঙ্গে ইতিপূর্বে বাঙালির কোনো পরিচয় ছিল না। তাই এই বিভ্রান্তি ও অভিভূতি আজ তাদের পেয়ে বসেছে। এক্ষেত্রে ইতিহাসবিদ মনীষী ইবন্ খলদুনের মূল্যবান মন্তব্য স্মরণ করলে আজকের দিনেও আমরা হয়তো উপকৃত হব। ইবন্ খলদুন বলেছেন–ধর্মশাস্ত্রকে মানুষ নিজের বৈষয়িক স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে টুকরো টুকরো করে কাজে লাগায়–তাতে ধর্মও মাহাত্ম্য হারায়, কাজও নষ্ট হয়। ১
এ-ও স্মর্তব্য যে আজ বিজ্ঞান দূরকে করেছে নিকট, তাই দেড় হাজার মাইলের ব্যবধান সত্ত্বেও দুটো বিচ্ছিন্ন দেশ নিয়ে পাকিস্তানরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সমস্বার্থে সহযোগিতা ও সহঅবস্থানের ভিত্তিতে অকৃত্রিম ও অকপট প্রীতির পরশে পরকে ভাই করার সাধনা না করলে তা টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না।
কল্যাণ অন্বেষা
সুস্থ মানুষ যেমন পথ্যাপথ্য বিচার করে না, সুস্থ জাতিও তেমনি কথায় কথায় শাস্ত্র আওড়ায় না। প্রাণ-প্রাচুর্যের এমন একটি আনন্দিত প্রেরণা আছে, যে-প্রেরণাবশে মানুষ সহজে ও স্বচ্ছন্দে আনন্দ অন্বেষায় ও কল্যাণ সাধনায় আত্মনিয়োগ করে। প্রাণের প্রেরণাতেই এ প্রয়াস চলে বলে তা স্বাস্থ্যকর। স্বাস্থ্য শিশুকে চাঞ্চল্য দান করে, আর চাঞ্চল্য বশে সে দুরন্ত হয়। এই দুরন্তপনাকে যে। ভয় করে, সে বস্তুত সুস্থতাকেই ভয় পায়। কেননা তাতে তার কাজ বাড়ে, ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে আলস্যের স্বস্তি উপভোগে অভ্যস্ত জীবনে একে সে বিপর্যয় বলেই জানে।
অর্জন যে করতে জানে না, বর্জনের শক্তি তার আয়ত্তে থাকে না। আয় না থাকলে মানুষ ব্যয় করতে ভয় পায়। গ্রহণ-বিমুখ মানুষ স্বাভাবিক কারণেই বর্জন-বিমুখ হয়। বৃষ্টি কিংবা বরফের দাক্ষিণ্য না-পেলে স্রোতস্বিনী যেমন বদ্ধ জলাতে জীর্ণতা পায়, তেমনি গ্রহণ-ভীরু মানুষও রক্ষণশীল হয়। শিশু-পাঠ্য কবিতার কলি মনে পড়ছে :
যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে।
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে।
যে জাতি জীবনহারা অচল অসার
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।
ঘরোয়া পরিবেশে প্রাপ্ত পুরুষানুক্রমিক বিশ্বাস-সংস্কার ও আচার-আচরণকে যারা জীবনের পরম আশ্রয় বলে মানে, তারা জগতের নিত্য-নব আলো-বাতাসকে অস্বাস্থ্যকর বলে জানে। তাই নতুনের প্রভাব এড়িয়ে প্রথার-প্রতাপ স্বীকার করে তারা জীবনযাত্রায় স্বস্তি খোঁজে। এমন ব্যক্তি বা সমাজ শামুকের মতো। তার কায়িক বৃদ্ধি আছে, মনের বিকাশ নেই। এমন মানুষ ভোগলিন্দু হয় কিন্তু চরিত্রবান হয় না। তাই ব্যবহারিক জীবনে সে স্বাচ্ছন্দ্যকামী, এবং এ স্বাচ্ছন্দ্যের ঈহা তাকে চুরি, মিথ্যাচার, লাম্পট্য, শোষণ, পীড়ন প্রভৃতি সর্বপ্রকার অপকর্মে প্রবর্তনা দেয়, এবং বস্তুজগতে সে বিদেশী বিজাতির আবিষ্কৃত নতুন সামগ্রী গ্রহণে হয় উৎসুক। তখন হারাম-হালালের, সুন্নত নফলের, মকরুহ্-বেদাঁতের কোনো বাছ-বিচার তার মনে জাগে না। কেবল জ্ঞান ও চিন্তার ক্ষেত্রেই সে শাস্ত্রীয়-প্রত্যয় পরিহার করতে নারাজ। শাস্ত্র হচ্ছে বিশ্বাসের ইমারত। বিশ্বাস মাত্রই আবেগসঞ্জাত। এবং আবেগ যুক্তির বীজও নয়, প্রসূনও নয়। তাই বিশ্বাস বিচ্ছিন্নতা ও বিরোধের বীজ বুনে। আর জ্ঞান মিলন-ময়দানে আহ্বান জানায়। কেননা, জ্ঞানে কুহেলিকা কিংবা কুয়াশা নেই, জ্ঞান প্রতারিত করে না। অতএব জ্ঞানের ক্ষেত্রেই কেবল মানুষ মিলতে পারে। আর জ্ঞান সব সময়েই বিপন্মুক্ত।
এক হিসেবে বিশ্বাস মাত্রেই অন্ধ। কেননা বিশ্বাসের জন্ম অনুমানে, লালন আবেগে এবং বিস্তার অনুভবে। অন্ধ যখন পথ চলে, তখন সে হাতড়িয়ে চলে এবং অনিশ্চিতে পা বাড়ায়। চক্ষুষ্মনের মতো চলার স্বাচ্ছন্দ্য এবং দেখার আনন্দ সে পায় না। অন্ধ প্রয়োজনের অনুগত। আনন্দ থাকে তার অনায়ত্ত। জ্ঞানই চক্ষু আর বিশ্বাস হচ্ছে অন্ধতা। জ্ঞানকে যে বিশ্বাসের উপরে ঠাই দেয় না, যে বিশ্বাসকে পরিহার করে জ্ঞানকে গ্রহণ করে না, তার জিজ্ঞাসা নেই। সে জগৎ ও জীবনের প্রসাদ থেকে বঞ্চিত। দেহ- প্রাণ প্রকৃতির দান বটে, কিন্তু চেতনা-সুন্দর জীবন জ্ঞানের প্রসূন। প্রকৃতির দান উদ্ভিদ কেবল অরণ্যই সৃষ্টি করে। মানুষের পরিচর্যায় গড়ে উঠে উদ্যান। তেমনি জ্ঞানের অনুশীলনে পাই সাংস্কৃতিক জীবন–যা সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের আধার। জ্ঞান মানুষকে বোধিসত্তায় উত্তীর্ণ করে। আসলে বোধিসত্ত্ব অর্জনই তো মানুষের লক্ষ্য। আর কে-ই-বা অস্বীকার করবে যে চিত্ত-সম্পদ ও বস্তু-সম্পদ–মানব-সাধ্য এই দুটো ঐশ্বর্যই জ্ঞানেই কেবল লভ্য? . সচেতন কিংবা অবচেতন ভাবে মানুষের যা কাম্য, কবির ভাষায় তা–
চাই স্বাধীনতা চাই পক্ষের বিস্তার
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার,
পরাণে স্পর্শিতে চাই ছিঁড়িয়া এ বন্ধন
অনন্ত এ জগতের হৃদয় স্পন্দন।
শাস্ত্র ও সংস্কারের বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্ত করা কেবল জ্ঞান ও যুক্তির জোরেই সম্ভব। কেননা জ্ঞান এবং যুক্তিই শুধু মানুষকে সুস্থ ও স্বস্থ করতে ও রাখতে পারে। জ্ঞানই চক্ষু এবং যুক্তিই চেতনা, এবং চেতনা-সম্পন্ন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি আত্মসামর্থ্যে পথ চলে, তাই সে চলার স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ দু-ই পায়।
আজ দেখছি শাস্ত্র ও সংস্কারের আনুগত্য এবং অশিক্ষিত মানুষের সংখ্যাধিক্যের সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক কর্মীরা দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করে প্রতারণার জাল বুনছে। নির্বাচনের সময়ে তাদের দেশ-জাত-ধর্ম-চেতনা এমনি প্রবল ও প্রচণ্ড হয়ে উঠে যে সরল মানুষেরা মনে করে বুঝি আমরা সর্বনাশের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি! এদের দস্তান না ধরলে বুঝি অপমৃত্যু সুনিশ্চিত! তারা কেবল কথার বেড়া দিয়ে শাস্ত্রের ও স্বার্থের, স্বত্বের ও স্বর্গের, সম্পদ ও স্বাচ্ছন্দ্যের এমন অনুপম মায়ালোক নির্মাণ করে যে বিমূঢ় অভিভূত অজ্ঞ মানুষের এই মরীচিৎকার খপ্পর এড়ানোর উপায় থাকে না।
সহজ করে বুঝতে গেলে, গণতান্ত্রিক সরকার হচ্ছে একটি প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপক সমবায় সংস্থা। রাষ্ট্রবাসীর ব্যবহারিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য দানই তার মুখ্য কাজ। বস্তু-সম্পদে রয়েছে মানুষের ব্যবহারিক প্রয়োজন এবং তজ্জাত সামাজিক অধিকার। আর চিত্ত-সম্পদ চিরকালই ব্যক্তিক। অতএব ব্যবহারিক প্রয়োজনে বৈষয়িক বস্তু-সম্পদের বারোয়ারী প্রয়োগ সুনিয়মিত রাখা ও সুনিয়ন্ত্রিত করাই হচ্ছে সরকার নামের সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য। এই সরকারি সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য কতকগুলো বিভাগে বিন্যস্ত; যেমন স্বরাষ্ট্র বিভাগ, অর্থ বিভাগ, বাণিজ্য বিভাগ, যোগাযোগ বিভাগ, বৈদেশিক সম্পর্ক বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, সৈন্য বিভাগ প্রভৃতি।
কোথায় রেলপথ করা দরকার, পাটের বাজার কোথায় সন্ধান করা উচিত, কলেরা-বসন্ত নিরোধের উপায় উদ্ভাবন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ কিংবা সেচ ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি একান্তই ঐহিক ও ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কিত বিষয়। মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের এসব সম্পদ ও সমস্যার সঙ্গে শাস্ত্র ও সংস্কারের কোনই সম্পর্ক নেই। এখানে আদর্শের কোনো প্রয়োজন যদি থাকে, তবে তা বিবেকী আদর্শ। এবং সে-আদর্শ সদিচ্ছার, সর্বজনীন কল্যাণের ও জৈব-স্বাচ্ছন্দ্যের। এ কার্যে যা প্রয়োজনীয় তা আদর্শ নয়, বরং অভিপ্রায় ও উপায়। বারোয়ারী কল্যাণে সদুপায় উদ্ভাবন ও প্রয়োগই কেবল দরকার, আর কিছু নয়।
এ যুগে সে উপায় হচ্ছে বিজ্ঞান ও প্রকৌশলবিদ্যা, আর অভিপ্রায় হচ্ছে সংহত ভুবনে জাতিপুঞ্জের সমস্বার্থে সহ-অবস্থান ও সহযোগিতার সদিচ্ছা। জাহাজ আরোহীরা যেমন স্ব স্ব জীবনের নিরাপত্তার জন্যেই জাহাজের নিরাপত্তা কামনা করে, তেমনি স্ব-স্বার্থেই মানুষ রচনা করবে মিলন-ময়দান, কামনা করবে সহ-অবস্থান ও সহযোগিতার জন্যে বিশ্বমানবতা ও বিশ্বশান্তি। এক্ষেত্রে শাস্ত্র, সংস্কার কিংবা তত্ত্বের প্রভাব ও প্রয়োগ অকল্যাণকর। একে তো শাস্ত্র ও সংস্কার রাষ্ট্রিক বিষয়-সংপৃক্ত নয়, দ্বিতীয়ত আজকের দিনে কোনো রাষ্ট্রেই নাগরিকরা অভিন্ন জাত-বর্ণ ধর্মের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব শাস্ত্র, সংস্কার কিংবা তত্ত্বকে এই ব্যবহারিক জীবনের সম্পদ ও সমস্যার সঙ্গে, দায়িত্ব ও কর্তব্যের সঙ্গে সংলগ্ন করা গলগ্রহ করারই নামান্তর।
পদলোভী স্বার্থবাজের ছল-চাতুরী ও বঞ্চনা-প্রতারণা থেকে দেশবাসীকে উদ্ধার ও রক্ষণের জন্যে আজ বিবেকী মানুষের বড় প্রয়োজন। এমন তীব্রতায় এদেশে ত্রাণকর্তার প্রয়োজন আগে আর কখনো অনুভূত হয়নি। আজ এমন কতকগুলো সংবেদনশীল মানববাদী কবি-সাহিত্যিক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক কর্মীর প্রয়োজন, যাঁরা ব্যক্তিগত জীবনে ত্যাগ ও নির্যাতন স্বীকারের অঙ্গীকারে এগিয়ে আসবেন সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে বিবেকী আত্মার ভূমিকা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবার জন্যে। আমাদের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তেমন মানববাদী কী এখনো দুর্লভ থাকবেন!
খাদ্য-সঙ্কট : বিশ্বসমস্যা
০১.
মানুষের জীবন নির্ঘ কিংবা নির্বিঘ্ন হবে এমন আশা কেউ করে না। কেননা নিজের জীবনের উপর সর্বাত্মক অধিকার মানুষের নেই। প্রকৃতির দেয়া রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু ছাড়াও সীমিত শক্তিতে মানুষ প্রাকৃতিক রোদ-বৃষ্টি-ঝড়-বন্যা প্রভৃতির প্রতিকূলতার সঙ্গে সব সময় পেরে উঠে না। তাছাড়া জীবিকার জন্যে সম্পদ প্রয়োজন এবং সম্পদ অর্জনে ও রক্ষণে রয়েছে নানা সমস্যা। আর সমস্যা মাত্রেই কমবেশি যন্ত্রণা। কাজেই নির্বিঘ্ন আনন্দও বাস্তবাতীত।
অতএব জীবনে কেবল সম্পদ ও আনন্দই কাম্য হলেও সমস্যা ও যন্ত্রণাকে এড়িয়ে তা পাওয়া সম্ভব নয়। অভাবিত নয় বলে এর জন্যে মানুষমাত্রেরই মানস-প্রস্ততি থাকে। অবশ্য এক্ষেত্রেও মানুষ কখনো স্বেচ্ছায় ও সহজে আত্মসমর্পণ করতে চায়নি। তাই ক্রমে এই প্রাকৃত শক্তিকেও সে জয় করেছে, বশ করেছে এবং দাসও করেছে। এক্ষেত্রে তার সাফল্য গর্বের ও গৌরবের, বিস্ময়কর ও মহিমময়।
কিন্তু আজ অবধি মানুষ যা করতে পারেনি, তা হচ্ছে তার প্রবৃত্তি-বশ্যতা থেকে বিবেকের মুক্তিসাধন। তাই অধিকাংশ মানুষ আজো জৈব প্রয়োজনের অনুগত জীবই রয়ে গেছে, প্রাণ-ধর্মের বশ্যতায় প্রাণী হয়েই আছে, বিবেক-চালিত বুদ্ধির আনুগত্যে মানুষ হয়ে উঠেনি। মানুষের বারো আনা দুঃখের উৎস এখানেই। মনুষ্য জীবনের যন্ত্রণার ও Tragedyর কারণ এ-ই। প্রকৃতির কোলে লালিত পিঁপড়ে থেকে হাতি অবধি কোনো প্রাণীকেই সম্ভবত খাদ্যাভাবে প্রাণ হারাতে হয় না। কেবল সমাজ-লালিত মানুষকেই হয়তো আদমের আমল থেকেই অনাহারে মরতে হয়েছে। অজন্মার ফলে যে খাদ্যাভাব তাতে হয়তো খুব কম মানুষই প্রাণ হারিয়েছে। চিরকাল প্রবল দুরাত্মার হাতে বঞ্চিত বুভুক্ষু মানুষই মরেছে লাখে লাখে। বেঁচে থাকার বিড়ম্বনা ও মৃত্যুর নিশ্চয়তাই তাদের হয়েছে ললাটলিপি।
সব মানুষের বুদ্ধি থাকে না, বিদ্যে হয় না, দৈহিক সামর্থ্য থাকে না, মানসিক যোগ্যতা থাকে না, চরিত্রও গড়ে উঠে না। তাই বলে তাকে বাঁচার অধিকার থেকে প্রাণের দাবি থেকে বঞ্চিত করবার বা রাখবার কারণ হতে পারে না এসব। মানুষকে জীব হিসেবে প্রাণী হিসেবেই বাঁচতে দেওয়া মানুষের নৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক ও মানবিক দায়িত্ব ও কর্তব্য।
সহযোগিতা ও সহ-অবস্থানের শর্তে সমাজ গড়েছে মানুষ। কিন্তু তার পরিবর্তে প্রবল মানুষ চিরকাল দুর্বল মানুষকে শোষণ করেছে, লুণ্ঠন করেছে এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে হত্যা করেছে। এই সহযোগিতা ও সহ-অবস্থানের সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভের আশায় মানুষ গোষ্ঠী-চেতনা, গোত্রীয়। ঐক্য, দৈশিক সংহতি, জাতীয়-মৈত্রী ও রাষ্ট্রিক কর্তব্য প্রভৃতির বোধ-বুদ্ধি জাগানোর সাধনা করেছে চিরকাল।
কিন্তু লক্ষ্য মহৎ হলেও উপায় শুভকর ছিল না। তাই জীবন-প্রতিবেশ সরল ও সুন্দর করতে গিয়ে বার বার জটিল ও বীভৎস করেছে। এজন্যে মানুষের ইতিহাস মুখ্যত প্রবলের পীড়ন-শোষণ ও হননের ইতিকথা–শোণিত-শোষণ ও রক্তপাতের করুণ কান্না। আজো এই ভুল পথের মরীচিকাই তাদের টানছে। স্বাধৰ্ম, স্বাজাত্য ও স্বারাষ্ট্র চেতনা ও মমতা নিয়ে আজো মানুষ জীবন সাধনায় ও স্বাচ্ছন্দ্য-সন্ধানে নিরত।
আজকের পৃথিবীই ধরা যাক। যেসব রাষ্ট্র শিল্পে-বাণিজ্যে-বিজ্ঞানে ও সামরিক শক্তিতে প্রবল, সেগুলো নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের বর্বর উল্লাসে মত্ত। অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য বিস্তারে ও রক্ষণে তারা সদাব্যস্ত। মাকড়সার জালবদ্ধ পতঙ্গের মতো, অক্টোপাস কবলিত প্রাণীর মতো বিশ্বের অনুন্নত ও দুর্বল রাষ্ট্রগুলো অনুপম ও অননুভূত মৃত্যু যন্ত্রণায় ধুকছে। যন্ত্রও যে এ যন্ত্রণার উপশমে সমর্থ নয়, তা তারা আজো উপলব্ধি করেনি। তাই যন্ত্রযোগে শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারেই তারা মুক্তি খোঁজে। কিন্তু বিশ্বের সব দেশগুলো যদি শিল্পায়িত হয়, তাহলে বানিজ্য করবে কার সঙ্গে? তখন তো কারো পুকুরের পানি কেহ নাহি খায় অবস্থা হবে। তখন পণ্য বিনিময়ে সমস্যা দেখা দেবেই। কেননা তখন পারস্পরিক প্রয়োজনে সঙ্গতি থাকবে না। শিল্পায়িত য়ুরোপ আজ সে মহাসমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে এবং আফ্রো-এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোকে শোষণ করে আত্মরক্ষার প্রয়াসে হয়েছে উদ্যোগী–এরই নাম য়ুরোপীয়ান কমনমার্কেট।
কিন্তু এভাবে কয়দিন চলবে! জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। এমনি জনসংখ্যার চাপে ষোলো শতকে য়ুরোপীয়রা রাক্ষসের ক্ষুধা, দস্যুর প্রবৃত্তি ও অক্টোপাসের কৌশল নিয়ে ছুটে বেরিয়েছিল বাঁচবার তাগিদে, আরো আগে যেমনটি করত মধ্য-এশিয়ার শক-হুঁন-ইউচিরা, তাতার-মোঙ্গলেরা। তখন তাদের ভাগ্য ভালোই ছিল। এশিয়া-য়ুরোপ তখনো ছিল বসতিবিরল। তাই মধ্য-এশিয়ার জনগোষ্ঠী ঠাই করে নিতে পেরেছিল সহজেই। ষোলো-শতকের য়ুরোপীয়দের ভাগ্যও ছিল প্রসন্ন। বসতি-বিরল তিন-তিনটে মহাদেশ আবিষ্কৃত হয়ে তাদের বাঁচার পথ করে দিল। বিগত পাঁচশ বছর ধরে তারা বাঁচল সম্পদে, গৌরবে ও ঐশ্বর্যে স্ফীত হয়ে।
কিন্তু এবার সে-সুযোগ কল্পনাতীত। অবশ্য গ্রহ-লোলাকে যদি কোনো ব্যবস্থা হয়ে যায়, তবে, তো কথাই নেই। এশিয়া-য়ুরোপে জনসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, জন্মনিয়ন্ত্রণে তার সমাধান নেই। সমাধান নেই কেবল কম্যুনিজমেও। কেননা জনসংখ্যার সঙ্গে ক্ষেত-খামারের আনুপাতিক ভারসাম্য রক্ষা করা কোনো মতেই সম্ভব হচ্ছে না। যদিও রাষ্ট্রগুলো বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে–অস্ত্রের ও অর্থের জোরে, যান্ত্রিক যোগ্যতায় ও বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনায় বেঁচে থাকার সাধনা করছে; তবু এতে শেষ রক্ষা হবে না। এখনকার জীবন ও জীবিকার আদর্শ হচ্ছে : সেই পুরোনোজোর যার মুলুক তার কিংবা যোগ্যতমের ঊর্ধ্বতন-নীতি। কিন্তু এ-সব নীতি এ যুগে স্থায়ী ফলপ্রসূ হবে না। কেননা অজ্ঞতা ও নিয়তিবাদের যুগ অপগত। এ যুগের সচেতন মানুষ বাঁচার তাগিদেই নাস্তিক ও নির্ভীক, উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল।
বিশেষ করে বিজ্ঞান ও প্রকৌশল-বিরল সামন্ত-যুগে সম্পদগত যে-স্থিতিশীলতা সম্ভব ছিল, ভূমি-নির্ভর জীবনে ও জীবিকায় নিয়তির মতো যে অমোঘতা ছিল, যে অবিচলিত সংস্কারাচ্ছন্নতা ও বিশ্বাসপ্রবণতা ছিল, তা আজ অবসিত। বিশ্বাস-সংস্কার আজ দেউলে–কোনো প্রবোধ, কোনো ভরসা, কোনো ভীতি, কোনো আশ্বাসই তা আজ দান করতে পারে না।
অতএব এ যুগে আনুগত্য নেই, নেই দাসত্ব। প্রতিবাদ-প্রতিরোধের আশঙ্কাহীন কোনো শোষণ-পীড়ন এ যুগে অসম্ভব। এ যুগে শুধু মার, শুধু হনন, শুধু কাড়ার সুযোগ তিরোহিত। এ যুগে কেবল দ্বিপক্ষীয় মারামারি, কাড়াকাড়ি ও হানাহানি চলতে পারে ও চলে। কিন্তু এতে কোনো পক্ষেরই কল্যাণ নেই। কারণ দুর্বলকে যারা কাড়ে, যারা মারবার যোগ্যতা রাখে, যারা হত্যা করেই নিশ্চিন্ত ও নির্দ্বন্দ্ব-নির্বিঘ্ন হতে চায়, তারা নিজেদের মধ্যেই লুণ্ঠিত সম্পদ ও শোষিত শোণিত নিয়ে কাড়াকাড়ি ও হানাহানি করে সুন্দ-উপসুন্দের পরিণাম পায়।
একটি অনূদিত কোরিয়ো কবিতা আজ বড় ভাল লাগল, যদিও অনুবাদ ভাষার দৈন্যে সুষ্ঠু ও সুন্দর নয়, কল্পনায় মূল্যের সৌন্দর্য আস্বাদন করে তৃপ্ত হয়েছি। কবিতাটি এখানে তুলে ধরছি :
এসো আমার কাছে, বলছি এসো তাড়াতাড়ি, আগুন লেগেছে ঘরে, সোনার বাড়িতে আগুন, সবুজ পাহাড়ে আগুন, গোলাপী ফুলের বাগান জ্বলছে, আর আমাদের প্রতিবেশীরা, বন্ধু প্রতিবেশীরা কেঁদে কেঁদে প্রাণভয়ে চলে যায়, ঘরগুলি খালি করে যায়।
নেকড়ে বাঘেরা গর্জন করছে, মেষের দল কাঁপছে, আর নেকড়ের দল গর্জায় আর হুঙ্কার দেয় আর একে অন্যের মাংস ছিঁড়ে নেয়, রক্ত ঝরে যায়। তারা হত্যা করে আর নিহত হয়। নিশ্চয় নেকড়ের দল নিজেরা ঝগড়া করে ধ্বংস হয়ে যাবে। রক্তাক্ত এ রাত্রি, কিন্তু আকাশে জ্বলছে তারা। তারাদল রয়ে যাবে, আর এখানা উঠছে। তাই বলি, এসো তাড়াতাড়ি.–দুজনে যাব মাঠে, পোড়ামাটি আবার চষবো তুমি আর আমি; আর আমরা বুনব ফসল। পাহাড় আবার সবুজ হবে, আর সাজাব আবার গোলাপী ফুলের বাগান।… ইত্যাদি। [নীল আকাশের নিচে : পাক দ্যু-জিন, অনুবাদ : জাহাঙ্গীর চৌধুরী, কোরিয়ার কবিতা, পৃ. ৪১]
অর্থ-গৌরবে, বাস্তব চিত্রে, আশাবাদে ও আত্মপ্রত্যয়ে এ কবিতা ঋদ্ধ। কিন্তু এই আশা ও আত্মপ্রত্যয় খণ্ডদৃষ্টি প্রসূত। কেননা আজ মানবিক সমস্যার সমাধান দেশগত বা রাষ্ট্রায়ত্ত নয়। নেকড়েরা আত্মকলহেই মরবে ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আহতরাও আর কখনো দগ্ধ মাটিতে ফসল ফলিয়ে প্রাচুর্য সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে না। এককভাবে য়ুরেশিয়ার কোনো রাষ্ট্রই আর স্বনির্ভরতায় বাঁচতে পারবে না। কেননা এখানে খাদ্যাভাব অনিবার্য। Common market বা ক্যুনিজম আজো সাময়িক সমাধান দিতে পারে বটে, কিন্তু বিশ্বের মানুষকে জীবনের অপরিহার্য অভাব মিটিয়ে শান্তিতে ও স্বচ্ছন্দে বাঁচতে হলে যৌথ প্রচেষ্টায় অন্য উপায় বের করতেই হবে। মানববাদকে মুখ্য করে সংহত ও সংযত জীবনে দীক্ষা নিতে হবে। Equitable-distribution of population & Food–পৃথিবীব্যাপী জনসংখ্যার ও খাদ্যবস্তুর সমবন্টনেই আপাতত এ সমস্যার দৃষ্টিগ্রাহ্য সমাধান নিহিত। গোত্র-বর্ণ-জাত-ধর্ম চেতনার উর্ধ্বে উঠে এশিয়া-য়ুরোপের বাড়তি মানুষকে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, আফ্রিকা ও আমেরিকায় ঠাই করে দিতে হবে। সর্বপ্রকার স্বাতন্ত্র ও বিদ্বেষ অতিক্রম করে কেবল মানববাদকে আদর্শ করে এগিয়ে আসতে হবে সমাধানের সন্ধানে। তা হলেই কেবল মানুষকে অপঘাত, অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করা যাবে।
অবশ্য বর্তমানে এ সমাধান মানব-প্রবৃত্তি বিরোধী ও অসম্ভব বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এই একমাত্র উপায়, যা করলে মানুষ আরো কয়েক শতাব্দী নিশ্চিন্তে কাটাতে পারবে। নইলে বাঁচবার প্রেরণায় মানুষ পরাক্রান্ত হয়ে বন্যার বেগে দিগ্বিদিকে ছুটে বের হবে আর হানাহানি করে যাদবকুলের মতো, শাক্যগোত্রের মতো ধ্বংস হবে।
আত্মঘাতী এ সংগ্রামে আত্মনাশ অনিবার্য। আত্মসংহারে এ আত্মনিবাশ আসলে বাঁচার সংগ্রামের ছদ্মবেশে। আজ তার লক্ষণ সর্বত্র দৃশ্যমান। বাঁচবার জন্যেই মারবার ও মরবার এ প্রবৃত্তি জৈবিক-পাশবিক বটে, কিন্তু অমানবিক। কেবল জীবের মতোই যদি আচরণ করবে, তা হলে হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্র সাধনার, প্রেম-প্রীতি-ন্যায়-নীতি অনুশীলনের কী প্রয়োজন ছিল! আজই বা এত ভাব-ভাবনার ও এত মহৎ বুলি কপচানোর সার্থকতা কী!
.
০২.
জন্মনিয়ন্ত্রণের মূলে রয়েছে দেশগত সমাধান প্রয়াস। কিন্তু এভাবে সমস্যা এড়ানোর প্রত্যাশা আপাতত বিজ্ঞতার পরিচায়ক হলেও জনসংখ্যায় স্থিতিশীলতা রক্ষা করা কঠোর আইন প্রয়োগ সাপেক্ষ। এবং এ আইন যে নীরবে সবাই মেনে নেবে, তাও মনে করার কারণ নেই। এক্ষেত্রেও বিদ্রোহ সম্ভব। আকাক্ষার কথা বাদ দিলেও এর সঙ্গে নৈতিক ও মানবিক প্রশ্ন জড়িত। সেদিন এক বন্ধু বলছিলেন : জন্ম নিয়ন্ত্রণে আস্তিক মানুষের স্রষ্টা-দ্রোহিতাই প্রকাশ পায়। কেননা, স্রষ্টাকে পালনকর্তা হিসেবে সে কার্যত অস্বীকার করে। তাঁর মঙ্গলময়ত্বে সে আস্থা হারায়। তার চোখে তিনি রাজ্জাক নন।
তাছাড়া এর মধ্যে একটা হীন আত্মসর্বস্বতা আছে। নিজের সুবিধের জন্যে অন্যের অস্তিত্ব প্রাপ্তির স্বাভাবিক অধিকার হরণ করা অমানবিক। আমরা ভাবছি, নিয়ন্ত্রণাভাবে অসংখ্য উদর-সর্বস্ব প্রাণী আমাদের মুখের গ্রাসে ভাগ বসাবে। তাতে আমরাও মরব, তারাও বাঁচতে পরবে না। কিন্তু এ সঙ্গে আমরা ভাবীকালের সক্রেটিস-এ্যারিস্টটল-প্লেটো, ফ্রয়েড-ডারুইন-আইনস্টাইন, কান্ট হেগেল-নীৎসে, মার্কস-লেনিন-মাওকেও তো হারাচ্ছি। যারা হয়তো এ সমস্যার অভাবিত সমাধান দিতে পারত!
এ ধারণার বিরুদ্ধে অবশ্য দুটো প্রবল যুক্তি রয়েছে।
এক, মানুষ মুখে যা-ই বলুক, জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে সে কখনো ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুগত থাকেনি। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে সে সবসময় বিধাতার দেয়া রোগ-শোক-জরা-মৃত্যু এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছে। সবকিছু অমোঘ জেনেও সে অনমনীয় রয়েছে–আত্মসমর্পণের আত্ম-স্বাতন্ত্র হারায়নি; এদিক দিয়ে সে চিরকাল প্রতিবাদী ও প্রতিরোধ প্রয়াসী–এভাবেই সে নিজের জন্যে কৃত্রিম জীবন ও জীবন প্রতিবেশ রচনা করেছে। এরই নাম সংস্কৃতি, সভ্যতা ও মনুষ্যত্ব। কাজেই জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রয়াসে নতুন কোনো বিদ্রোহ নেই।
দুই. জীবনের অন্য অনেক প্রাণীর মতো মানুষও আত্মরক্ষার ও আত্মবিস্তারের গরজে চিরকাল জিঘাংসু। অন্য প্রাণীকে তো নয়ই, স্বজাতি মানুষকেও সে কখনো কৃপা করেনি। কাজেই সহচর মানুষকে যে হত্যা করতে পারে, অভব-অদৃশ্য সম্ভাব্য মানুষের সৃষ্টি-রোধ করার মধ্যে তার কোনো নিষ্ঠুরতা নেই। হীন-স্বার্থপরতা যা রয়েছে তাও তুলনায় অতি তুচ্ছ। আর মহৎ মানুষ প্রাপ্তির আশায় সৃষ্টির দ্বার অবারিত রাখা জুয়াকে জীবিকা করার মতোই বিড়ম্বনাকে বরণ করা মাত্র।
অবশ্য এর পরেও প্রশ্ন থেকে যায় : জাত হিসেবে মানুষ কী আরো মহৎ হতে পারে না? তবে Destructive-এর চেয়ে Preventive measure-ধ্বংসাত্মক উপায়ের চেয়ে বারণাত্মক বা নিরোধাত্মক পদ্ধতিই কাম্য।
আপাতত, জন্মনিয়ন্ত্রণে, সমাজতন্ত্রে ও সাম্যবাদে জীয়নকাঠির সন্ধান চলবে বটে, কিন্তু এই দেশগত বা রাষ্ট্রগত খণ্ড প্রয়াসে স্থায়ী সমাধান নেই। একক বিশ্বে সহযোগিতা, সহঅবস্থান ও বিশ্বব্যাপী খাদ্য ও খাদকের সমবণ্টনের মধ্যেই স্থায়ী কল্যাণ ও ভাবী মানব-ভাগ্য নিহিত।
জাতি গঠনে ভাষার প্রভাব
আত্মীয়তা ও ঐক্যের বন্ধন হিসেবে রক্ত-সম্পর্কের পরেই ভাষার স্থান। গভীরভাবে বিবেচনা করলে মনে হবে ভাষার গুরুত্ব রক্ত-সম্পর্কের চাইতেও বেশি। কেননা, বোধগম্য ভাষার মাধ্যমেই হয় জানাজানি ও মন দেয়া-নেয়া। অপরিচয় যেমন অনাত্মীয়তার নামান্তর, তেমনি পরিচয় মানে চাক্ষুষ করা নয় বরং পরস্পরের মন-মেজাজ ও মত-পথ জানা। এটি কেবল কথার মাধ্যমেই সম্ভব। অতএব, অর্থপূর্ণ ধ্বনিই মানুষের ব্যষ্টি জীবন ও সামষ্টিক-সামাজিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে। ভাষার মাধ্যম ব্যতীত আমরা যেমন ভাবতে পারিনে, তেমনি ভাষা ছাড়া আমরা নিজেদেরকে অনুভব করতেও অসমর্থ। কাজেই চেতনা প্রকারান্তরে ভাষারই অন্য নাম। মানুষের মানসিক কিংবা বৈষয়িক জীবন তাই ভাষানির্ভর। বলতে গেলে, অন্য প্রাণী থেকে মানুষ যে উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে, তার মন-বুদ্ধি-আত্মার যে বিকাশ ও বিস্তার হয়েছে, তা মুখ্যত ভাষার কারণেই এবং গৌণত তার কায়িক-সৌকর্যের দরুণ। অসংখ্য ধ্বনি-সৃষ্টির শক্তি ও হাত প্রয়োগের সামর্থ্যই রয়েছে তার যাবতীয় বিকাশের মূলে।
প্রেম-প্রীতি-স্নেহ, ঘৃণা-বিদ্বেষ-অবহেলা প্রভৃতির উদ্ভব আর অবসানও অনেকখানি নির্ভর করে কথার উপরই। ব্যক্তিগত জীবনে ভাষার মাধ্যমে পরিচয় না ঘটলে রাগ বা বিরাগ জন্মাবার কারণ সহজে মেলে না। অতএব, রক্ত-সম্পর্ক ও ভাষার অভিন্নতাই পারস্পরিক মিলনের আদি ভিত্তি। অভিন্ন ভাষাই আদিকালে বিভিন্ন গোত্রের সমবায়ে সমাজ গঠনের সহায়ক হয়েছে।
ভাষার মাধ্যমেই ভাব-চিন্তার বিকাশ ঘটে বলেই সৌজন্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বৃদ্ধিরও মুখ্য অবলম্বন হয়েছে এ ভাষাই। স্বভাষার বিকাশবিরহী কোনো মানবগোষ্ঠীই সভ্য নয়। কেননা, ভাষার মাধ্যমেই শ্রেয় ও প্রেয়বোধ সমাজে বিস্তার লাভ করে। অভিন্ন ভাষার মাধ্যমেই বিচ্ছিন্ন গোত্রগুলো পরস্পরের সন্নিহিত হয়ে সংহত ও সঙ্ঘবদ্ধ জীবন-ভাবনায় ও জীবন-রচনায় ব্রতী হয়।
জন্মসূত্রে মানুষ যে ভাষা পায় অর্থাৎ আশৈশব মানুষ যে ভাষায় অভ্যস্ত হয়, সেটিই তার স্বভাষা বা মাতৃভাষা। ঐ ভাষাই তার চেতনার নিয়ামক বলে তার প্রাণেশ্বর হয়ে উঠে। অতিক্রান্ত শৈশবে পড়ে-পাওয়া ও শুনে-শেখা ভাষা ঐ ভাষার মতো চেতনা- সংপৃক্ত হয় না, প্রিয়ও হয় না। ফলে স্বভাষী ব্যতীত অন্যভাষী লোকও প্রীতির ক্ষেত্রে আনুপাতিক দূরত্বে অবস্থান করে।
বিদ্বানেরা বলেন, মানুষের বাকযন্ত্রে কোনো ধ্বনিই অবকল ভাবে দ্বিরুক্ত হতে পারে না। প্রতি মুহূর্তেই তা পরিবর্তিত হচ্ছে। কায়িক অসামর্থ্যই তার মুখ্য কারণ। যেহেতু প্রতি মানুষেরই রয়েছে। স্বতন্ত্র অবয়ব, সেহেতু কোনো দুটো মানুষের ধ্বনি-সৃষ্টির শক্তি অভিন্ন নয়। তাছাড়া অজ্ঞতা ও অনবধানতাবশেও ধ্বনি বিকৃত হয়। অতএব, দৈহিক অসামর্থ্য ও অজ্ঞতাই ধ্বনি-বিকৃতির কারণ। ভাষার ক্ষেত্রে এই বিকৃতিকে আমরা সৌজন্যবশে বিবর্তন বা রূপান্তর বলে থাকি। একটা পরিমিত দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে এই বিবর্তনটা স্পষ্ট হয়ে উঠে। অর্থাৎ চার-পাঁচ পুরুষের ব্যবধানে তা কানে ধরা দয়। এমনি করেই এক মূল ভাষা বিবর্তিত হয়ে অসংখ্য বুলি ও ভাষাতে পরিণত হয়। আমাদের আর্য ভাষাও এমনি করেই এশিয়া-য়ুরোপে অসংখ্য ভাষা হয়ে বিশিষ্ট বিকাশ লাভ করেছে।
ঋগ্বেদের আমলের ভাষার ক্রমবিবর্তনে গড়ে উঠেছে উত্তরভারতের আধুনিক ভাষাগুলো। বাঙলাও এদের একটি। ভাগলপুর থেকে কক্সবাজার, মালদহ থেকে গোয়ালপাড়া অবধি এ ভাষার লেখ্যরূপ আজো অভিন্নরূপে চালু রয়েছে। কিন্তু আঞ্চলিক বুলি হয়েছে বিচিত্র ও স্বতন্ত্র। বুলিতে বুলিতে পার্থক্য এত বেশি যে, আনাড়ির চোখে এদের গৌত্রিক অভিন্নতা সহজে ধরা পড়ে না। অতএব কেবল লেখ্যরূপের মাধ্যমেই ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতির উদ্ভব সম্ভব হয়েছে। এ লেখ্যরূপের উদ্ভব বিলম্বিত হলে আমরা আজকের বাঙালি জাতিকে এত বড় ভূখণ্ডে আজকের সংখ্যায় পেতাম না।
প্রমাণস্বরূপ বলা যায়, এক সময় মাগধী-প্রাকৃত চালু ছিল বিহারে, উড়িষ্যায়, বাঙলায় ও আসামে। মাগধী প্রাকৃতের ক্রমবিকৃতিতে উদ্ভূত হয় অবহরে। তখনো আঞ্চলিক পার্থক্য তেমন প্রকট ও প্রবল হয়ে উঠেনি। তাই লেখ্য অবহট্ট ছিল এসব অঞ্চলে অভিন্ন। প্রাকৃত-পৈঙ্গল, দোহাকোষ প্রভৃতিই তার প্রমাণ। আরো পরে অর্বাচীন অবহট্ট যুগেও লেখ্যরূপে আনুগত্য ছিল অবিচল। তাই চর্যাগীতিতে পাই বঙ্গ-কামরূপ ও বিহার উড়িষ্যার পদকার।
একচ্ছত্র শাসনই অভিন্ন লেখ্য ভাষার উদ্ভবের মুখ্য কারণ। দশ শতক.অবধি মোটামুটিভাবে এসব অঞ্চল গুপ্ত ও পাল শাসনে ছিল। তাই অর্বাচীন অবহট্ট যুগেও ভাষিক ঐক্য দৃশ্যমান। পালরাজত্বের অবসানে এই রাষ্ট্রিক ঐক্য বিঘ্নিত হয়। তাই যদিও তেরো শতক অবধি বাঙলা উড়িষ্যা এবং ষোলো শতক অবধি বাঙলা-আসামী অভিন্ন ছিল, তবু একচ্ছত্র শাসনের অর্থাৎ এককেন্দ্রিক শাসন-সংস্থার অনুপস্থিতির দরুন অর্বাচীন অবহট্ট-উত্তর ভাষা সর্বজনীন লেখ্যরূপ। পায়নি। তাই আঞ্চলিক বুলিই স্থানিক প্রয়োজনে লেখ্য ভাষায় উন্নীত হয়। ফলে বিহারে, উড়িষ্যায়, . বাঙলায় ও আসামে চালু হল চারটি স্বতন্ত্র লেখ্য ভাষা। আর এর সুদূরপ্রসারী ফল এই দাঁড়াল যে মাগধী প্রাকৃত ভাষী একটি ভাষিক জাতি বা সম্প্রদায় কালে চারটি ভাষিক জাতিতে পরিণত হল। যদি গুপ্ত ও পাল আমলের মতো একচ্ছত্র শাসন আধুনিক বুলিগুলোর স্বরূপ প্রাপ্তির সময়ে ও লেখ্যরূপ গ্রহণকালে চালু থাকত, তাহলে বিহার, উড়িষ্যা, বাঙলা ও আসাম জুড়ে একটি বিরাট ভাষিক জাতি গড়ে উঠতে পারত, এবং তাহলে আর্থিক, রাজনৈতিক কিংবা সাংস্কৃতিক শক্তিরূপে পূর্ব-ভারতে একটি মর্যাদাবান রাষ্ট্রের স্থিতি অবধারিত ছিল। কিন্তু একচ্ছত্র শাসন-সংস্থার অভাবে তা হতে পারেনি এবং আর কোনদিন হবেও না। অবশ্য অভিন্ন ভাষা দিয়ে যে একক রাষ্ট্র গড়ে উঠবে এমন নিশ্চয়তা আগেও কখনো ছিল না, এখনো নেই। তবে এ-কথা সত্য যে এমনি পরিবেশ সংহতির ও একক রাষ্ট্রগঠনের অনুকূল।
বাঁকুড়া ও চট্টগ্রামের এবং মালদহ ও গোয়ালপাড়ার মানুষ যে একই লেখ্য ভাষার বন্ধনে ধরা দিয়েই বাঙালি হয়েছে, এ সত্য অস্বীকার করবার উপায় নেই। নইলে তাদের স্থানিক বুলি এতই পৃথক যে তারা কোনক্রমেই অভিন্নভাষী জাতি হতে পারত না। মালদহ কিংবা বাঁকুড়ার লোক সহজেই হতে পারত বিহারী, যেমন মেদিনীপুরের লোক হতে পারত উড়িয়া এবং সিলেটীরা হত আসামী। কাজেই আজকের বাঙালির স্বাজাত্যবোধের উৎস স্বভাষা। কেননা এ জাতি পরিচয়ে নৃতত্ত্ব, গোত্রচিহ্ন, ধর্মমত ও বর্ণবিন্যাস অস্বীকৃত। এমনকি আঞ্চলিক অভিমানও এক্ষেত্রে অবহেলিত। তাই পুরেনো রাঃ, সুম্ম, সমতট, বরেন্দ্র, বঙ্গ, গৌড় প্রভৃতি গোত্রবাচক ও অঞ্চল নির্দেশক পরিভাষাগুলোও আজ অবলুপ্ত।
এককালের অবজ্ঞেয় যে বঙ্গ সেই নামেই সব কয়টি অঞ্চল হয়েছে সংহত। যদিও লেখ্য ভাষাটি রূপ নিয়েছে দক্ষিণ রাঢ়ের বুলি ভিত্তি করেই। মুঘল আমলে প্রায়ই বিহার-উড়িষ্যাও যুক্ত থাকত বাঙলার শাসন-সংস্থার সঙ্গে। বস্তত ১৯০৫ সন অবধি সুবে বাঙ্গালাহ বা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি ছিল বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে। এ ব্যবস্থা যদি পাল আমলের পরেও চালু থাকত, তা হলে সেই সুবে বাঙ্গালাহই হত আজকের বাঙালির স্বদেশ বা মাতৃভূমি। কেননা, তা হলে লেখ্য ভাষারূপে রাজধানী অঞ্চলের বাঙলাই গৃহীত হত সর্বত্র। এবং সে ভাষা হত সবারই মাতৃভাষা। কারণ, ইতিহাসের সাক্ষ্যে প্রমাণিত যে, দেশে লেখ্য ভাষার অনুপস্থিতির সুযোগে বহিরারোপিত ধর্মের কিংবা বহিরাগত শাসকের ভাষা শাসিত-অঞ্চলে লেখ্য ভাষারূপেও স্থায়িত্ব লাভ করে। যেমন আমরা বাঙালিরা কেউ আর্য ছিলাম না। আমরা অস্ট্রিক ও ভোটচীনার রক্ত-সঙ্কর মানুষ। আমাদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে একসময় অস্ট্রিক (দ্রাবিড়) ও মঙ্গোলীয় বুলি চালু ছিল। কিন্তু উত্তরভারতীয় ধর্ম ও লেখ্য ভাষা গ্রহণ করে আমাদের পূর্বপুরুষেরা স্বভাষা ও স্বাজাত্য পরিহার করে বিস্মৃত হয়ে আর্যত্বের মিথ্যা গৌরব-গর্বে স্ফীত হয়েছিল। ফলে আমাদের নৃতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র, গৌত্রিক অভিমান, মাতৃভাষার মমতা, জীবনযাত্রার রীতিনীতি প্রভৃতি সবকিছু সানন্দে বিসর্জন দিয়ে হয়তো তারা আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিল।
নৃতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র ও গো-চেতনা বিলুপ্তির পক্ষে ধর্মের চেয়ে ভাষার প্রভাব যে অধিক এবং অমোঘ ফলপ্রসূ, তা দুনিয়ার অন্যত্রও দেখতে পাই। এখনকার আরব জাতি বলতে ইরাক থেকে জিব্রাল্টর অবধি বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের অধিবাসীদেরই নির্দেশ করে, অথচ তারা আদিতে এক গোত্রীয় কিংবা অভিন্ন ভাষী ছিল না–বেবেলীয়, কালদীয়, আশিরীয়, ফিনিশীয়, হিত্তি, কপ্ট, অর্য, শক, হুন প্রভৃতি নানা পুরোনো স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সমবায়ে গড়ে উঠেছে এ আরব জাতি। এবং তা ধর্মের অভিন্নতায় সম্ভব হয়নি, ভাষার ঐক্যেই নির্মিত হয়েছে। আজকের য়ুরোপীদের কিংবা ল্যাটিন আমেরিকানদের জাতি-চেতনাও রক্ত-নির্ভর নয়–ভাষাভিত্তিক।
যারা ভাষিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে, তাদেরকে অভিন্ন ধর্মের বন্ধন কিংবা অভিন্ন ভৌগোলিক সংস্থিতি অপরের মধ্যে আত্মমিশ্রণে প্রেরণা দেয়নি। তারা অন্যদের সঙ্গে থেকেও স্বতন্ত্র। অন্যভাষীর সঙ্গে সহঅবস্থান করেও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে অসংলগ্ন। বিগতকালের য়ুরোপে এবং আধুনিক ভারতে, কানাডায়, আফ্রিকায় ও ল্যাটিন আমেরিকায় এটিও সামাজিক অথবা রাষ্ট্রিক বিরোধের ও বিপর্যয়ের মুখ্য কারণ। আজকের পাকিস্তানও এ সমস্যা থেকে মুক্ত নয়। পশ্চিম পাকিস্তানে সিন্ধি, বেলুচ এবং পাখতুন অসন্তোষও মূলত ভাষিক স্বাতন্ত্র্যজাত অর্থাৎ এর যতটা ভাষিক স্বাতন্ত্র্য চেতনা প্রসূত, ততটা আঞ্চলিক ব্যবধানগত কিংবা গোত্ৰ-চেতনাজাত নয়। পাঞ্জাবের সারাইকী-ভাষী মুলতানীদের সাম্প্রতিক মনোভাবও আমাদের এ ধারণার সমর্থক। পূর্ব বাঙলার সাম্প্রতিক বাঙালি-বিহারী দ্বন্দ্বেরও উৎস এই ভাষাই। তাই পশ্চিম বাঙলা থেকে আগত উদ্বাস্তুদের চিহ্নিত করা যেমন দুঃসাধ্য, বিহারীদের স্বজন বলে গ্রহণ করা তেমনি দুষ্কর। ভাষাগত ঐক্য ও স্বাতন্ত্রই এই মিলন ও বিরোধের, এই আপন-পর পার্থক্যের মূলে ক্রিয়াশীল, বলতে গেলে আজকের দুনিয়ার তাবৎ মানুষ বর্ণ-সঙ্কর বা রক্ত-সঙ্কর। বিচিত্র কারণে যুগ যুগ ধরে যাযাবর মানুষ স্থানান্তরে গেছে, নিঃশেষে মিশে গেছে স্থানীয় মানুষের মধ্যে, এবং ভাষার ঐক্যে গড়ে তুলেছে সংহত সমাজ। যেখানে ভাষা অভিন্ন হয়ে উঠেনি, সেখানে বিরোধ-বিদ্বেষ চিরন্তন হয়ে রয়েছে। প্রমাণস্বরূপ বলা চলে আমাদের দেশে বলখী, সমরখন্দী, বোখারী, খোরাসানী, সবজওয়ারী, সিরাজী, নিশাপুরী, মক্কী, মদনী, হেজাকী, ইয়ামিনী কিংবা সৈয়দ, কোরাইশী, ফারুকী, সিদ্দিকী, উসমানী, আলাভী, ফাতেমী প্রভৃতি দেশ-গোত্র জ্ঞাপক ও আভিজাত্য সূচক কুলবাচির আধিক্য সত্ত্বেও ভাষাগত ঐক্যের কারণে জাতি পরিচয়ে এগুলো বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। এবং পাকিস্তানীর জন্যে এক সাধারণ ভাষা নির্মাণের আড়ালেও রয়েছে এই অভিপ্রায়।
.
০৪.
আদিকালের ধর্মপ্রবর্তক, শাসক এবং সাম্রাজ্যবাদীদের এ তত্ত্ব জানা ছিল, তাই তারা দীক্ষিত মানুষকে, বিজিত জাতিকে, শাসিত জনগোষ্ঠীকে স্বভাষা গ্রহণে বাধ্য, প্ররোচিত কিংবা অনুপ্রাণিত করত। এমনি প্রয়াস ও রেওয়াজ আজকের দিনেও দুর্লভ নয়। পাকিস্তানে উর্দুভাষা ও হরফ চালু করার পশ্চাতে ছিল এমনি অভিসন্ধি। আজ উপনিবেশিক প্রতিবেশ ও সাম্রাজ্যবাদ অবসিত। কাজেই প্রবলের এই প্রবণতাও আজ নিষ্ফল ও নিষ্ক্রিয়। বৈদিক, ল্যাটিন, ফরাসি, আরবি ও আধুনিক ইংরেজি ভাষা এমনি করেই স্বগোত্রের মানুষে ও অঞ্চল-বহির্ভুত ভু-খণ্ডে ভাষিক আধিপত্য বিস্তার করেছে।
অবশ্য ধর্মপ্রবর্তকেরা, শাসক-সাম্রাজ্যবাদীরা নিজেরাও দীক্ষিত ও বিজিত জনের ভাষা শিখতে পারতেন, কিন্তু তাতে তাদের উদ্দেশ্য সাধিত হত না। নিজেদের ভাষার মাধ্যমে নিজেদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাস ও দর্শনের সঙ্গে শাসিতদের পরিচয় ঘটিয়ে শাসকদের প্রতি একপ্রকারের অনুরাগ ও আনুগত্য সৃষ্টি করা সম্ভব। এভাবে শাসকদের অন্তরঙ্গ পরিচয়-মুগ্ধ অনুরাগী ও অনুগত প্রজাগোষ্ঠী বিদেশী-বিজাতি শাসকের প্রতি সহিষ্ণু হয়ে উঠে। ইংরেজ আমলে আমাদের শিক্ষিতশ্রেণীর ইংরেজ এবং ইংরেজি সাহিত্য, দর্শন ও সংস্কৃতি-প্রীতি এ সূত্রে স্মর্তব্য। ভাষা ছাড়া অন্য কোনো কিছুর মাধ্যমে এই অনুরাগ ও সহিষ্ণুতা সৃষ্টি করা সম্ভব হত না। কেননা, কেবল বাহুবলে প্রভাব ও প্রতাপ চালু রাখা চলে না। কেননা, যেখানে মন জানাজানির উপায় নেই, সেখানে সমঝোতা ও প্রীতি অসম্ভব। অপরিচয়ই অপ্রীতি ও অসহিষ্ণুতার উৎস। এসব কারণেই সম্ভবত বা অন্যতম ব্রহ্মরূপে পরিকীর্তিত।
.
০৫.
আবার বাঙালির কথাই বলি। লেখ্য বাঙলার প্রভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের লোক বাঙালি জাতিরূপে সংহত হল বটে, কিন্তু ভাষিক ও ধর্মীয় ঐক্য সত্ত্বেও আঞ্চলিক দূরত্বের দরুন আচারে-সংস্কারে, মনে-মননে, জীবন-ভাবনায় ও রীতি-নীতিতে পার্থক্য সুপ্রকট হয়ে বিদ্যমান ছিল। এই আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতার প্রভাব আঠারো শতক অবধি নির্বিঘ্ন ছিল। উনিশ শতকে যান্ত্রিক যানবাহন চালু হওয়ার ফলে এবং মুখ্যত মুদ্রণ-শিল্পের দ্রুত বিকাশের বদৌলতে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে সংহতি ও সান্নিধ্যের সুযোগে, আর প্রতীচ্য বিদ্যা ও সংস্কৃতির প্রভাবে বাঙালির সেই আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য আজ লুপ্তপ্রায়।
এভাবেই বাঙালি শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে, ইতিহাসে, দর্শনে, আচারে, আচরণে, ধ্যানে ও ধারণায় অভিন্ন হয়ে উঠেছে ও আজো উঠছে। মধ্যযুগের সাহিত্য- শিল্প এবং ঘরোয়া আচার-সংস্কার ও রীতি-নীতিই এর সাক্ষ্য। সাহিত্য ক্ষেত্রে আমরা দেখছি, ধর্মমঙ্গল কেবল উত্তর রাঢ়ের সম্পদ; তেমনি বৈষ্ণব সাহিত্যের বিকাশও কেবল পশ্চিমবঙ্গেই সীমিত, চণ্ডীমণ্ডপ ও চণ্ডীমঙ্গল রাঢ় অঞ্চলেই নিবন্ধ; তেমনি মনসা মঙ্গল ও লোকগীতিকা পূর্ববঙ্গেরই ঐশ্বর্য, বাউল-সহজিয়া মতের প্রভাব ও প্রসার-ক্ষেত্র হয়েছে উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গ। প্রণয়োপাখ্যানের উদ্ভব হয়েছে চট্টগ্রাম বিভাগে। খাদ্যবস্তুর রন্ধন প্রণালীর আঞ্চলিক রকমফের যেমন ছিল; দারু, কারু ও চারুশিল্পেরও তেমনি স্থানিক বিকাশই কেবল সম্ভব ছিল। শাস্ত্রনিরপেক্ষ আচার-সংস্কারের ক্ষেত্রেও ছিল স্থানিক পার্থক্য। আসবাব-তৈজসেও ছিল আঞ্চলিক রূপ। কাজেই কোনো কিছুই ভৌগোলিক বাধা অতিক্রম করে দেশময় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়তে পারেনি। গ্রামীণ জীবনে রীতিনীতির এ পার্থক্য আজো নিশ্চিহ্ন হয়নি। তবু অন্তত হাজার বছর ধরে লেখ্য ভাষার মাধ্যমে এ অঞ্চলের মানুষ এক অবিচ্ছেদ্য আত্মীয় সমাজ গড়ে তুলছে যার আধুনিক নাম বাঙলা দেশ ও বাঙালি। অতএব অভিন্ন ভাষাই জাতি-চেতনার অকৃত্রিম ভিত্তি ও জাতি-নির্মাণের মৌল উপাদান। আর সবকিছুই কৃত্রিম এবং তাই স্বল্পস্থায়ী। অর্থাৎ ভৌগোলিক ঐক্য, ধর্মীয় অভিন্নতা, মতবাদের একতা, রাষ্ট্রিক বন্ধন ও গোত্রিক পরিচয় কখনো অকৃত্রিম জাতি গড়ে তুলতে পারে না–অন্তত অতীতে কোনো দিন পারেনি।
নজরুল-জিজ্ঞাসা
প্রিয়জন ও শ্রদ্ধাভাজনের গুণকীর্তন ও দোষ-খণ্ডন মানব-স্বভাব। শ্রদ্ধাবানেরা একে পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করেন। ভাল কবিতার কবি এবং ভাল কাজের কর্তাও প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয়। কাজেই তার কথা বলতে আবেগজাত অভিভূতি, শ্রদ্ধাপ্রসূত দোষগুপ্তি এবং পক্ষপাত দৃষ্টি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠে। কেননা, অনুরক্ত মাত্রই অনুগত হয়। অনুরাগ স্বভাবতই আনুগত্য দান করে। তাই সব জনপ্রিয় কবি-লেখক কিংবা সমাজ-ধর্ম-রাষ্ট্রনেতা সম্বন্ধেই অনুরাগীরা প্রশস্তিমুখর ও বিচারবিমুখ।
কিন্তু সাধারণ মানুষের স্বভাব যা-ই হোক, ঐতিহাসিকের কিংবা সমালোচকের ভূমিকায় যারা অবতীর্ণ, তাদের পক্ষে এ দুর্বলতা দায়িত্ব ও কর্তব্যভ্রষ্টতা। এ দুর্বলতা যারা অতিক্রমণের সামর্থ্য অর্জন করেননি, তাঁদের পক্ষে লেখনী ধারণ অনুচিত। কারণ বাস্তব প্রতিবেশে সত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেয়াই ঐতিহাসিক ও সমালোচকের দায়িত্ব। মিথ্যার প্রলেপে ক্রুর ও রূঢ় সত্য আবৃত করলে ইতিহাস ও সমালোচনার ফলশ্রুতিলব্ধ প্রাপ্তি ও প্রজ্ঞা থেকে সমাজ বঞ্চিত থাকে। ফলে চেতনার ও মননের জ্ঞানজ বিকাশধারা হয় বিকৃত। না বললেও চলে যে খণ্ড ও ভুল জ্ঞানের চাইতে অজ্ঞতা শতগুণে শ্রেয়। উপকার করবার অধিকার সবার থাকলেও ক্ষতি করার অধিকার স্বীকৃতি পায় না। ঐতিহাসিক ও সমালোচক হবেন সত্যসন্ধ, ন্যায়নিষ্ঠ ও বিবেকানুগত। আমাদের ঐতিহাসিক ও সমালোচকদের মধ্যে এসব গুণ বিরলতায় দুর্লক্ষ্য।
কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রসঙ্গেই এ ভূমিকাটির অবতারণা। আমাদের পূর্ব বাঙলায় নজরুল আজকাল বহুল আলোচিত ঘরোয়া কবি। প্রবন্ধের তো সংখ্যাই নেই, তার সম্বন্ধে লেখা বড় ছোট বইয়ের সংখ্যাও দিনদিন বেড়ে চলেছে। কিন্তু সে অনুপাতে আমাদের নজরুল সম্পর্কে জ্ঞান ও বোধ বৃদ্ধি পাচ্ছে না বরং বিভ্রান্তি বাড়ছে। তার মুখ্য কারণ, সমালোচনা যে অংশত গবেষণাও এবং সমালোচককে প্রয়োজনমতো যে, ঐতিহাসিক আর গবেষকের দায়িত্বও পালন করতে হয়, তা আমাদের সমালোচকগণ যেন স্বীকার করেন না। তাই তত্ত্ব ও তথ্য, সত্য ও শ্রুতি, স্মৃতি ও সদিচ্ছা, বাস্তব ও কল্পনা তাদের চোখে একাকার এবং ভালকথা ও সত্যকথা তাঁদের কাছে একই মূল্যে বিকায়। প্রতিজ্ঞায় (Promise-এ) যদি ভুল থাকে, সিদ্ধান্ত সত্য হতে পারে না। অঙ্গীকারে গলদ সিদ্ধান্ত অসার্থক করবেই। প্রস্তাবের ফাঁকির দরুন প্রাপ্তিতে প্রবঞ্চনার ফাঁক থাকবেই।
কবিও মানুষ। তাই তারও রয়েছে গৃহগত জীবন, তাঁরও মন-মেজাজ গড়ে উঠে ধার্মিক, আঞ্চলিক, সামাজিক, শৈক্ষিক, আর্থিক ও প্রতিবেশিক প্রভাবে। কাজেই এই পারিবেশিক পটে অর্জিত চেতনার পরিপ্রেক্ষিতেই আত্মপ্রকাশ করে মানুষ তার প্রাত্যহিক আচরণে। অতএব, ব্যবহারিক কিংবা মানসিক কোনো অভিব্যক্তিই স্থান-কাল প্রসূত চেতনা-নিরপেক্ষ নয়। কবি-কৃতি বুঝবার জন্যে যার মন-মননের সন্ধান নিচ্ছি, তার মন-মনন কখন কোথায় কেমন করে লালন পেয়েছে, তা যদি না জানি তাহলে সিদ্ধান্ত মিথ্যা হতে বাধ্য। খণ্ডদৃষ্টি কেবল খণ্ড সত্যের সন্ধান দিতে পারে এবং খণ্ড সত্য মিথ্যারও অধম এবং ক্ষতিকর।
নজরুল সম্বন্ধীয় গ্রন্থের নাম যদিও নজরুল চরিত-মানস, নজরুল-সমীক্ষা, নজরুল-প্রতিভা প্রভৃতি তবু এগুলোতে আবেগের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ যতখানি আছে, তথ্যবিচার ও সত্য নির্ধারণের প্রবণতা ততখানি নেই। ফলে সমালোচনাগুলো আলোড়িত আবেগ উঁচুমাত্রায় প্রকটিত করেছে বটে, যথার্থ মূল্যায়নের সহায়ক হয়নি।
নজরুলকে পাঠকের বোধগত করবার জন্যে যেসব গ্রন্থকার ও সংকলকের প্রয়াস, তাদের কাছেই তাদের বিবেচনা-প্রত্যাশায় নজরুল সম্পর্কিত আমদের কয়েকটি জিজ্ঞাসা পেশ করছি :
১. ১৮৯৯ সনের ১১ জ্যৈষ্ঠ যে নজরুল ইসলামের জন্ম–এ তথ্য কোনো প্রমাণে স্বীকৃত? একি পারিবারিক লিখিত কাগজ সূত্রে না বিদ্যালয়ে ভর্তির খাতার প্রমাণে?
২. সম্রাট শাহ আলমের আমলে এ পরিবার কোথা থেকে চুরুলিয়ায় এলেন? এঁরা কোন্ কাজীর বংশধর? শাহ আলমের আমলে বাঙলা দেশে বসতি করে দু-তিন পুরুষের মধ্যে বাঙালি হয়ে উঠেছে, তেমন ভদ্র পরিবারের নজির বিরল। বিশেষত পলাশীর যুদ্ধোত্তরকালে অবাঙালিরা উত্তরভারতের দিকেই হিজরত করছিল। সেখান থেকে তখন এদেশে লোক আসার সাক্ষ্য বিরল।
৩. দশ-এগারো বছর বয়সেই লেটোর দলের গান বাঁধার যোগ্যতা অর্জন স্বাভাবিক নয়। কচি বালকের প্রতিভার এমন বিকাশের তথ্য কোন্ সূত্রে সংগৃহীত?
৪. গায়ের গরিবের ছেলে নজরুল মাঝে মাঝে পড়া ছেড়েছেন, রেল-গার্ডের বাসায়, রুটির দোকানে চাকরিও করেছেন, অমনোযোগ ও উচ্ছলতার খবরও মেলে, তবু সতেরো-আঠারো বছর বয়সেই দশম শ্রেণীতে পড়ছেন, দেখতে পাই। এ-ই বা কোন্ যাদুবলে সম্ভব?
৫. চুরুলিয়ায় যখন ছিলেন, তখন নজরুল নিতান্ত বালক। সে বালকই ইমামতি করেছেন, আর মুসলমানেরা সেই বালকের মুবতদী হয়ে নামায পড়ছে–যোগ্যতা ও বৈধতার কোনো প্রশ্নই উঠল না?
৬. রেল-গার্ডের বাসায় নজরুল কী ঘটিয়েছিলেন?
৭. রুটির দোকানে নজরুল যে-কাজে নিযুক্ত (ময়দামাখা, রুটি-তৈরি ও বিক্রি) তাতে গান গাইবার অবকাশ ছিল কী? হারমোনিয়ামই বা সেকালের রুটির দোকানে যোগাড় হল কী করে?
৮. আলি আকবরের ভাগ্নী নার্গিস বেগম এখনো হয়তো জীবিতা এবং ঢাকাবাসিনী। সম্ভবত আলি আকবর সাহেবও জীবিত আছেন। তা ছাড়া কবি আজিজুল হাকিমের সঙ্গে পরে নার্গিস বেগমের বিয়ে হয়েছিল। আলি আকবর সাহেবের গায়েও তার শত্রু-মিত্রের অভাব নেই। নজরুলের জীবনীকার কিংবা কাব্য-সমালোচকদের কেউ এ যাবত সদ্য-বিয়ে-করা বউয়ের সঙ্গে নজরুলের বিচ্ছেদের কারণ সন্ধানে উৎসুক হননি। অথচ কোন্ কোন্ কবিতায় এ বিচ্ছেদ-বেদনার প্রভাব পড়েছে তাও আলোচিত হয়েছে। তাহলে এ ব্যাপারে তাদের এমন ঔদাসীন্যের কারণ কী?
৯, মা জাহেদা খাতুনের প্রতি সন্তান নজরুলের বিরূপতার কারণ আবিষ্কারেও কেউ উদ্যোগী হননি। মুসলিম সমাজে মা যদি চাচার কাছে নিকাহ্ বসে থাকেন, তাতে কী অন্যায় আছে যে লেখকগণ তা গোপন করতে চান? তাঁদের সঙ্কোচের ফলে এমন একটি নির্দোষ ব্যাপারও রহস্যময় হয়ে উঠে এবং পাঠকের মনে বীভৎস কল্পনা প্রশ্রয় পায়।
১০. নজরুল যখন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি, লিখে টাকা পাচ্ছেন, তখনও তার ঘন ঘন আর্থিক সঙ্কট দেখা দেয়ার কারণ কেউ উল্লেখ করেন না। গান বেঁধে কিংবা পত্রিকা সম্পাদক হয়েও তার অভাব ঘোচেনি, কিন্তু কেন? একি নেশা করতেন বলে?
১১. তার রোগের উৎপত্তি ও বিস্তারের কারণও কেউ চিকিৎসকদের থেকে জানবার চেষ্টা করেননি। এ রোগের লক্ষণও কেউ বর্ণনা করতে চাননি। একি নেশা করার পরিণাম?
১২. তাঁর বৃদ্ধা বিধবা শাশুড়ি গৃহগত কোন্ বিসম্বাদের ফলে নির্লক্ষ্য নিরাশ্রয় জীবন বরণ করলেন, তারও কোনো হদিশ মেলে না এদের আলোচনায়।
১৩. নজরুলের যদি ইসলামেই আস্থা থাকে, তাহলে কালী-সাধনার প্রেরণা পেলেন কী করে? আর ঘরোয়া জীবনে যদি তিনি কুসংস্কারপ্রবণ ও ভূত-ভীরু হন, তাহলে তার বিপ্লব-বিদ্রোহ মূলক কবিতা কিংবা আচারিক ধর্মবিরোধী বাণী কৃত্রিম ফরমায়েশী রচনা হয়ে যায় না কী?
১৪. তাঁর অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি তাঁর পারিবারিক আবহাওয়া হিন্দুয়ানী হয়ে থাকে, তাহলে তাঁর যে কোনো ব্যক্তিত্ব ছিল না, তা স্বীকার করতেই হয়। অথচ এসব নিদর্শন কোনো কেতাবে মেলে না।
১৫. স্ত্রী ও শাশুড়ির প্রভাবে ও প্রতাপে যদি হিন্দুয়ানীতেই তিনি সমর্পিত চিত্ত এবং সে কারণেই যদি ছেলেদের খত্না না করিয়ে থাকেন, তাহলে প্রমীলা নজরুলের চিতার বদলে কবর হল কী করে?
১৬. মানুষ নজরুলের চরিত্রে কী কোনো দোষ-দুর্বলত ছিল না কেবলই গুণ এবং সবই ছিল গুণ? সগুলোয় বর্ণনা থাকে না কেন?
১৭. তাঁকে পাকিস্তানের জাতীয় কবি বলেই প্রচার করা হয়। পাকিস্তান ও মুসলিম জাতীয়তা সম্বন্ধে তাঁর পরিব্যক্ত অভিমত নবযুগের সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও কবিতার আলোকে আলোচিত হয় না কেন?
এমনি নানা জিজ্ঞাসার পূর্ণাঙ্গ জবাব না থাকলে আলোচনা-সমালোচনা যে বৃথা ও ব্যর্থ তা উপলব্ধি করবার সময় আজ সমাগত। কেননা, কবি জীবনৃত। যেখানে জিজ্ঞাসা নেই, সেখানে উত্তরও অনায়ত্ত। আর উত্তরই যে জ্ঞান, তা কে না বোঝে! অতএব যে-প্রয়াস জ্ঞান দেয় না, বোধের বিকাশ ঘটায় না, তা পণ্ডশ্রম মাত্র। পাঠকের পক্ষে বিভ্রান্তিকর এমনি গ্রন্থরচনার উৎসাহ না-থাকাই শ্রেয় ও বাঞ্ছনীয়।
নববর্ষ
০১.
প্রবুদ্ধ মানুষের জাগ্রত জীবন প্রতি নববর্ষে নবজীবনের দ্বার উন্মুক্ত করে। যে-মানুষ দু:খী, যে-মানুষ জিজ্ঞাসু ও অন্বেষ্টা, সে-মানুষেরই আসে নবজীবনের আহ্বান। কেননা, সুখ ও তৃপ্তি বন্ধ্যা। দুঃখ ও আর্তিই কেবল সৃষ্টিশীল। সুখ ও তৃপ্তি লক্ষেই মানুষের জীবন-প্রয়াস নিয়োজিত বলেই সুখ ও তৃপ্তি স্বস্তি আনে এবং তখন প্রয়াসের প্রেরণা অবসিত হয়। বঞ্চিতের অভাববোধই অভিপ্রায় ও আকাঙ্ক্ষা হয়ে প্রয়াসে ও সগ্রামে রূপ পায়।
নববর্ষের পূর্বাশার নতুন সূর্য জাগ্রত মানুষের মনে নতুন আশা জাগায়। ভরসাপুষ্ট মানুষ হৃত অতীতের আচ্ছন্নতা ও অবসাদ পরিহার করে নবোদ্যমে এগিয়ে চলে উত্তরণের পথে সাফল্যের স্বর্ণমিনার লক্ষ্যে। তখন সে অকুতোভয়, আত্মপ্রত্যয়ে দুর্জয় ও অত্যুঙ্গ আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত। তখন তার অমিততেজ, অপরিমেয় উদ্যম। প্রতি নববর্ষে প্রবুদ্ধ-চেতনা উজ্জ্বল প্রাণবন্যার উত্তল ঊর্মি হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে চারদিকে। জাগিয়ে দেয় ও মাতিয়ে তোলে আধমরা, আধ-ভোলা বিকৃত চেতনার মানুষগুলোকে। বর্ষণের ছোঁয়া-লাগা দূর্বার মতো জেগে উঠে জীবন্ত মানুষ, প্রাণের সাড়া দোলা দিয়ে যায় চিন্তায় ও কর্মে। . নববর্ষ তাই নবজীবনের নকীব। নববর্ষ চেতনাকে ঢালাই করবার, চিন্তাকে ঝালাই করবার এবং ক্রটি শোধনের, ভ্রান্তি নিরসনের ও নব পরিকল্পনায় জীবন-রচনার আহ্বান জানায়। প্রতি নববর্ষ তাই এক-একটি জীবন-বসন্ত। হৃত-অতীতের সুপ্তি থেকে, গ্লানি থেকে, ব্যর্থতা থেকে, অনুশোচনা থেকে নির্জিত জীবনকে নববর্ষের বাসন্তী হাওয়ায় উজ্জীবিত করে চেতনার কিশলয়ে, চিন্তার প্রসূনে, প্রাণময়তার পরাগে মণ্ডিত করার লগ্নরূপে আসে এক-একটি নববর্ষ।
আমাদের জীবনে নববর্ষের প্রথমদিন আসে আমাদের জন্মদিনের মতো হয়ে। জন্মবার্ষিকী কিংবা বিবাহবার্ষিকীর দিনটি যেমন আনন্দের ও উৎসবের, মনের উপর এর যেমন একটি স্বপ্ন-মধুর ও অনুভূতি-সুন্দর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে, নববর্ষের প্রথম দিনও আমাদের প্রাণে তেমনি এক আনন্দ সুন্দর শিহরণ জাগায়। স্বল্প-অনুভূত এক অব্যক্ত মাধুর্যে, এক অস্ফুট উষার আভাসিত লগ্নের লাবণ্যে, এক সুদিনের অনুচ্চারিত আশ্বাসে আমাদের চিত্তলোক ভরে তোলে এই নববর্ষ।
.
০২.
মধ্যযুগেও আমাদের দেশে নববর্ষের উৎসব হত। শাসকগোষ্ঠীও উদ্যাপন করত নওয়োজ। কিন্তু আমাদের মধ্যযুগীয় চেতনায় এর গুরুত্ব যতটা বৈষয়িক ছিল, মানসিক ছিল না ততটা। তাই এর পার্বণিক প্রকাশ নিষ্প্রাণ রেওয়াজে ছিল সীমিত, কখনো তা মানস-বিকাশের সহায়ক হয়ে উঠেনি। স্থিতিশীলতার সাধক মধ্যযুগীয়, মানুষ তাই জন্মদিন পালন করত না, মৃত্যুদিবসই স্মরণীয় করে রাখবার প্রয়াসী ছিল। জন্মোৎসবে আমাদের আগ্রহ জাগে প্রতীচ্য প্রভাবে। জন্ম ও জীবনের মহিমা প্রতীচ্য প্রভাবেই আমাদের হৃদয়বেদ্য হয়ে উঠে। সেই থেকে বছরান্তে জন্মদিন কিংবা নববর্ষ আমাদের জন্যে নবজীবনের, নবজাগরণের ও নতুন আশার বাণী বয়ে আনে।
পাশ্চাত্য প্রভাব গাঢ় হওয়ার সাথে সাথে আফ্রো-এশিয়ার গণমনের সুপ্তি টুটে গেল, তখন জাগ্রত জীবনের চাঞ্চল্যে জন্ম নিল দুর্বার আকাঙ্ক্ষা। সম্ভাবনার প্রসারিত দিগন্তে মনবিহঙ্গ পক্ষ বিস্তার করল জীবনের অনন্ত তৃষ্ণাতৃপ্তির বাসনা নিয়ে। মন-চাতকের সে অভিসারে ছিল অভিযানের আয়োজন ও দাপট। কেননা অভিপ্রেত বর্ষণবিন্দু নির্বিঘ্নে লভ্য যে নয়, তা বোঝা কঠিন ছিল না। প্রলয়ঙ্কর ঝড়ের মুখেই যে অগ্রসর হতে হবে, তা তারা কেবল জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়েই নয়, প্রাণের মধ্যেও অনুভব করেছিল। সে ঝড় কালবৈশাখীর ঝড়; কালান্তরের, রূপান্তরের ও বিবর্তনের ঝড়–সেই যুগান্তকর বিপ্লবী ঝড় ভাঙল বিশ্বাস, টুটল সংস্কার, উড়িয়ে নিল অন্ধতা, ঝেটিয়ে নিল ভীরুতা, আরো নিল কত কত জান-মাল। সে-ঝড়ে আনল রক্তবন্যা, জাগাল রক্তোচ্ছাস। প্রাণের প্রেরণাপ্রসূত জীবনতৃষ্ণা তাতে আরো তীব্র হয়ে, তীরতীক্ষ্ণ সংকল্প হয়ে দুর্জয় করে তুলল গণমানবকে। তারই ফলে এ শতকের প্রথম সূর্যের কাল থেকে জাগ্রত গণমানব জগতের কোথাও না-কোথাও প্রতিদিন কোন-না-কোনো ক্ষেত্রে মরণপণ সংগ্রামে জয়ী হচ্ছে। সংগ্রাম চলছে পরাধীনতার বিরুদ্ধে, পীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে, অজ্ঞতার ও অবিদ্যার বিরুদ্ধে, দারিদ্র্য ও বৈষম্যর বিরুদ্ধে, অন্যায় ও অধর্মের বিরুদ্ধে। সংগ্রাম শুরু হয়েছে রোগ-জরা মৃত্যুর বিরুদ্ধে, প্রকৃতির কার্পণ্য ও রহস্যময়তার বিরুদ্ধে।
আমাদের দেশেও সংগ্রাম চলছে। সগ্রামী গণমানব আজ সুন্দর ও কল্যাণের অন্বেষ্টা। নৈতিক ও বৈষয়িক অধিকার প্রতিষ্ঠায় চেতনা-চঞ্চল মানুষ আজ সংগ্রাম-মুখর। কিন্তু তার মানস-নৈপুণ্য অশিক্ষাজাত অপ্রত্যয়ে আজো অনার্জিত ও অনায়ত্ত। তাই তার সগ্রাম বহুমুখী ও সর্বাত্মক হয়ে উঠতে পারেনি, পারেনি সে বিচিত্র ও বহুধা আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত হতে। তাই তার দুঃখ ঘোচেনি, সংগ্রাম পায়নি পূর্ণতা, সিদ্ধি রয়েছে অনায়ত্ত, সুখ-স্বস্তি-স্বাচ্ছন্দ্য রয়েছে দৃষ্টিসীমার বাইরে।
নববর্ষের প্রথম সূর্যের আলোয় তার সংগ্রামী সংকল্প ঝালাই করবার, দৃঢ়তর করবার সুযোগ আসে বৎসরান্তে একবার। এই শতকে পলাশ-লাল সূর্য মন ও মাটি রাঙিয়ে রাঙিয়ে নবজীবনের আলপনা এঁকে দিচ্ছে। দেশে দেশে ঘরে ঘরে সেই রাঙা-প্রভাতের প্রসাদ-পুষ্ট মানুষ তৈরি হচ্ছে, যারা রচনা করবে নতুন জগৎ ও মহিমান্বিত নবীন জীবন। মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান-মানববাদীর এই মন্ত্রে দীক্ষা নেবার লগ্ন হচ্ছে নববর্ষের প্রথম প্রভাত। প্রতি নববর্ষই মুক্তির প্রতীক। অজ্ঞতা, অন্ধতা, অবিদ্যা আর অন্যায়, পীড়ন, শোষণ, দারিদ্র্য থেকে কাম্য-মুক্তির প্রতিভূ প্রতিটি নতুন বছর। প্রতিটি নববর্ষ হচ্ছে মুক্তির প্রমূর্ত সংকল্প, শপথ ও সংগ্রাম। মানব-মুক্তি সংগ্রামে, মানবকল্যাণে আমার দেহ-মন-আত্মা নিয়োজিত হোক, সমর্পিত হোক–নববর্ষের প্রথম প্রভাতে এই দৃপ্ত শপথ স্মরণ করেই শুরু হোক এ বছরের জীবন।
.
০৩.
বিশ শতকের পলাশ-লাল সূর্য বিশ্বমানবের জন্যে মুক্তির বাণী বয়ে এনেছিল। সে-সূর্য আজো রোজ ভোরে খুন-রাঙা রূপ নিয়ে পূর্বাশায় উদিত হয়। বদ্ধ মানুষকে দেয় আশ্বাস ও অভয়, শোনায় আশার বাণী, পীড়ক-শোষকদের করে দেয় সতর্ক।
বিশ শতকের সূর্য প্রতি প্রভাতে মানুষের জন্যে মুক্তি বয়ে আছে। সে-মুক্তি আসে পরাধীনতা থেকে, অজ্ঞতা থেকে, অবিদ্যা থেকে, অশিক্ষা থেকে, কুসংস্কার থেকে, দারিদ্র্য থেকে, কাপুরুষতা থেকে, পীড়ন থেকে, শোষণ থেকে। দুনিয়ার কোথাও-না-কোথাও প্রতিদিন মানুষের জীবনের কোন-না-কোনো ক্ষেত্রে মুক্তি আসছে। এই সাফল্যে, এই আশ্বাসে ও এই প্রত্যয়ে মানুষ আজ বিদ্রোহী, সংগ্রামী ও আত্মপ্রত্যয়ী। আমাদের দেশ-দুনিয়ায়ও সে-রাঙা প্রভাত আসে। আমাদেরও আশ্বস্ত করে যায়। প্রতি নববর্ষে আমাদের প্রথম সূর্য আমাদেরও মনে জাগিয়ে তোলে রঙিন স্বপ্ন। প্রতি নববর্ষে আমাদের আকাশেও জাগে কালবোশেখী-নববর্ষের সওগাত ও আশীর্বাদ। তাতে আমাদের মধ্যে জাগে প্রাণের সাড়া। বন্দীর বেদনা, শোষিতের ক্ষোভ ঝড় হয়ে দেখা দেয়। তাতে মুছে যায় সব গ্লানি, খসে পড়ে জীর্ণতা, উড়ে যায় জড়তা, নতুন ভুবনে নব সৃষ্টির আশা ও আশ্বাসে ভরে উঠে বুক। উল্লসিত প্রাণপুরে জেগে উঠে গান :
ঐ নতুনের কেতন ওড়ে কাল-বোশেখীর ঝড়–
ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর প্রলয় নতুন সৃজন-বেদন
আসছে নবীন জীবনহারা–অসুন্দরের করতে ছেদন।
অতএব,
তোরা সব জয়ধ্বনি কর!
পদাবলী : কাম ও প্রেম
০১.
তত্ত্ববিদের চোখে যা-ই হোক, সাধারণের অনুভবে কামে ও প্রেমে পার্থক্য সামান্য ও বিজ্ঞানীর চোখে দু-ই নিরেট জৈবিক বৃত্তি। কৈশোর থেকে প্রৌঢ় বয়স অবধি মানুষ মাত্রেরই হৃদয়ে কাম প্রেমের লঘু-গুরু লীলা চালু থাকে। কাজেই কাম মানুষের প্রবলতম প্রবৃত্তি। সে-বৃত্তি অভিব্যক্তি পায় প্রেমরূপে এবং কখনো কখনো স্নেহ, প্রীতি ও ভক্তিরূপে। সবার চেতনায় প্রেমের প্রভাব থাকলেও সবার জীবনে প্রেম প্রকাশ ও বিকাশ পায় না। অবদমিত ও অবচেতন বাঞ্ছ তখন পরোক্ষ উপায় খোঁজে উপভোগের। শৃঙ্গার তথা রতিরস তাই কর্ম ও কলার মুখ্য অবলম্বন হয়েছে। এ কারণেই আদি মানুষের সমাজে Art ও Ritual ছিল অভিন্ন। অন্ন ও আনন্দ প্রয়াস, কর্ম ও ধর্ম সাধনা এক ধারায় ছিল একাকার। রাগ-বিরাগের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় গতি পেয়েছে জীবন।
আদি কৃষিজীবী সমাজে মৈথুন ছিল ফসল উৎপাদনের প্রতীক ও সহায়। পৃথিবীর বিভিন্ন অনুন্নত সমাজে আজো তা অবিলুপ্ত। এদেশে ধর্মগ্রন্থেই রয়েছে এ তত্ত্ব–বাজসনেয়ি সংহিতায়, ব্রাহ্মণে, বৃহদারণ্যকে, মহাভারতে ও ছান্দোগ্যে। এ তত্ত্বের ক্রমবিকাশে পাই সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র এবং সহজিয়া, বাউল, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপত্য, লিঙ্গায়েত প্রভৃতি ধর্মসম্প্রদায়। অতএব দেবতত্ত্বের ও মানবমনের বিকাশ ধারায় রূপ ও রতিবোধের দান গভীর ও ব্যাপক।
.
০২.
শিল্প-সাহিত্যের সব শাখাই রূপ ও রতিভিত্তিক। অন্যকথায় রূপ ও রতি একাধারে কারণ ও কার্য এবং বীজ ও ফল। এ দৃষ্টিতে রূপ ও রতির অনুধ্যানেরই প্রসূন মানুষের সংস্কৃতি ও সভ্যতা।
চিত্র ও মূর্তিশিল্প, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশিল্প, নাচ ও গান, কবিতা ও গাথা, ধর্ম ও দর্শন, রূপকথা ও উপন্যাস সবকিছুই ক্রমবিকাশ লাভ করেছে রূপ-রতি ভিত্তি করেই। বলতে গেলে মানুষের জীবনধারায় থাকে কাম ও প্রেমেরই বিচিত্র বিকাশ। এর প্রকাশ প্রতিবেশ-নির্ভর। সেজন্যে এর অভিব্যক্তি ও বিকাশ সরল ও একরঙা হয়নি। জীবন প্রবাহ ঝর্ণাধারার মতোই উপল ও বাঁক মেনে চলে। তাই জীবনে আসে বৈচিত্র্য, বিকৃতি ও বক্রতা।
জগতের শ্রেষ্ঠ চিত্র, মূর্তি, সাহিত্য, নৃত্য ও সঙ্গীত তাই প্রেম-প্রতীক। এক কী বহু ধর্ম আর দর্শনও প্রেমবাদী। পৃথিবীব্যাপী আদি সমাজে মানুষের মনে ও মননে, কর্মে ও ধর্মে শৃঙ্গারই পেয়েছে প্রধান্য। শৃঙ্গারের নামই তাই আদিরস। সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক বিশেষ স্তরে জীবনের ক্ষেত্রে এ আদিরসের বিচিত্র ও বহুধা প্রভাব স্বীকার করে ধন্য হয়েছে মানুষ, ধন্য করেছে দেবতাদের। গ্রীক ও হিন্দু পুরাণ তার সাক্ষ্য।
.
০৩.
পরকীয়াতেই প্রেমের স্ফুর্তি। তবু সমাজ-বিকাশের বিশেষ স্তরে সমাজে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যে, দাম্পত্য প্রেমকেই আদর্শ ও মহিমান্বিত করবার প্রয়াস চলল। এই নৈতিক চেতনার যুগেই আমাদের দেশে হর-গৌরী, ইন্দ্র-সচী, রাম-সীতা, বিষ্ণু-লক্ষ্মী প্রভৃতি দাম্পত্য প্রেমের মহিমা কীর্তনচ্ছলে নিজেদের প্রণয়াকুতি প্রকাশ করেছে মানুষ। এই কৃত্রিম প্রয়াসে মানুষের তৃষ্ণা মেটেনি, ভরে উঠেনি তার বুক। তাই আবার পরকীয়া রসে সিক্ত হয়েই প্রস্ফুটিত হল তার চিত্ত-উৎপল। এই রসেই তার হৃৎকমলে সঞ্চিত হল মধু, সৃষ্টি হল মহিমান্বিত। মানুষের অবদমিত ও অবেচতন বাঞ্ছা-অপূর্ণতার আকুতি গানে, গাথায়, গল্পে, কবিতায়, উপন্যাসে, চিত্রে, নৃত্যে, প্রতিমায়, অধ্যাত্ম জিজ্ঞাসায় আজো অভিব্যক্তি পাচ্ছে বিচিত্র ও বর্ণালী হয়ে।
ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, শিরি-ফরহাদ, কৃষ্ণ-নিপ্পিনাই বা রাধা-কৃষ্ণ–এ প্রেম প্রকাশের আদর্শ ও বিকাশের অবলম্বন হয়ে প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে মানুষের মনের আকুতি মিটিয়েছে। সমাজ-কলেবর বৃদ্ধির সাথে সাথে নৈতিক চেতনা যতই প্রবল হয়েছে, ততই সূক্ষ্ম অনুভবের স্তরে উন্নীত হয়েছে স্থূল প্রয়োজন, বাস্তব চাহিদা পেয়েছে মানসোপভোগে চরিতার্থতা। তাই বাস্তব জীবনে যা পাপ (sin), যা নৈতিক দোষ (vice) ও সামাজিক অপরাধ (crime) এবং সেহেতু ঘৃণ্য ও পরিহার্য; ভাবলোকে তা-ই আত্মার উল্লাস জাগায়। এ জীবনে কেবল আনন্দানুভবের উৎস হয়ে থাকেনি, পারিত্রিক সুখ-স্বপ্নেরও আধার হয়েছে।
দেহে রূপ, রূপে কাম, কামে প্রেম আর প্রেমেই আত্মার মুক্তি। সূফী-বৈষ্ণবের এ ধারণা একদিনে গড়ে উঠেনি। মানুষ অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছে চাওয়া ও পাওয়ার মধ্যে ব্যবধান থাকে বিস্তর, বাধা থাকে দুর্লঙ্ঘ। বাঞ্ছিত বস্তুমাত্রেই দুর্লভ ও দুঃসাধ্য। অথবা দুর্লভ না হলে কিছু বাঞ্ছনীয় হয় না। কাজেই তার জন্যে দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি ও প্রয়াস প্রয়োজন। ধৈর্য ও অধ্যবসায়ই এ সাধনার সম্বল। হৃদয়ে দাহ ও চোখে অশ্রু প্রেমিকের নিয়তি। আর মিলনাকাঙ্ক্ষা তথা বিরহবোধই তার প্রেরণা ও সামর্থ্যের উৎস। এইজন্যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য বিরহী আত্মার কান্নায় করুণ।
.
০৪.
এই রূপ ও রতি, কাম ও প্রেমবাঞ্ছা অভিব্যক্তি পেয়েছে রাধা-কৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলীতে। চৈতন্য-পূর্ব যুগে এগুলোতে অধ্যাত্মতত্ত্ব ছিল না। এ দৈহিক প্রেম ঐহিক জীবনে আনন্দিত স্বপ্ন জাগানোতেই ছিল সীমিত। চৈতন্যের প্রেম-ধর্ম প্রচারিত হওয়ার পরে এ সংগীত পারত্রিক ত্রাণের অবলম্বন হল। তখন অপ্রাকৃত হৃৎ-বৃন্দাবনে জীবাত্মা রূপিণী রাধার ও পরমাত্মারূপী কৃষ্ণের প্রণয়লীলার অনুধ্যান ও আস্বাদনই এর অপার্থিব মহৎ ও পরম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। এভাবে প্রেমকে তত্ত্বের অনুগত করে রাধাকৃষ্ণের অবৈধ প্রেমকে করা হল মহিমান্বিত ও অনন্য। চৈতন্য-পূর্ব যুগে গোটা ভারতব্যাপী যা ছিল শৃঙ্গার-রস উপভোগের বাহন, চৈতন্যোত্তরকালে তা-ই হল অধ্যাত্মরসের আকর।
জয়দেব, বিদ্যাপতি ও বড়চণ্ডীদাসের পদাবলী ছিল শারীর প্রেমের আকুতিমুখর। বৈষ্ণব ভক্তের চোখে পদকারেরা হলেন মহাজন ও গোস্বামী; আর পদাবলী হল সাধন-শাস্ত্র ও ভজন গীতি। তার পরে চৈতন্যোত্তর যুগের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক প্রায় সব সঙ্গীতই আধ্যাত্মরসাশ্রিত।
যদিও জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতবাসীরা রাধা-কৃষ্ণ, রাম-সীতা কিংবা হর-গৌরী বিষয়ক পদ অভিন্ন লক্ষ্যে রচনা ও আস্বাদন করেছেন, তবু তত্ত্বগত পার্থক্য যে ছিল না, তা নয়। কেবল দ্বৈতাদ্বৈতবাদে নয়, ভক্তি আর প্রেম তত্ত্বেও ছিল তফাৎ। দ্বিজ চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, দীনচণ্ডীদাস, মীরাবাই, তুলসীদাস, আবদুর রহীম খান খানান, দাদু, এয়ারী, দরিয়া, রজব, তাজবেগম, আহমদ, রসখান কিংবা চাঁদ কাজী সৈয়দ সুলতান, আলাউল, সৈয়দ মর্তুজা, আলিরজা, মীর ফয়জুল্লাহ্ প্রভৃতি পদের আধ্যাত্মিক তাৎপর্য তাই অভিন্ন নয়।
আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়, চৈতন্যদেব বাঙালির এবং ষোলো শতকের ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক গণ-নেতা। হয়তো বাঙলাদেশে থাকেননি বলেই বাঙলায় বৈষ্ণব ধর্মের বিস্তার আশানুরূপ হয়নি। কিন্তু তাঁর প্রেমবাদ, তাঁর সাম্য, প্রীতি ও করুণার বাণী, তাঁর উদার মানবতাবোধ বাঙালিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। গৌতম বুদ্ধের ও ইসলামের বাণীর ঐতিহ্য তার মাধ্যমে নতুন করে পেয়ে বাঙালি-চিত্ত সঞ্জীবিত হল। এজন্যে ষোলো শতক বাঙালির চিপ্রকর্ষের কাল–রেনেসাঁসের যুগ। আশ্চর্য, তবু ষোলো-সতেরো শতকে পদাবলী রচয়িতা বাঙলা দেশের সর্বত্র মিলে না। এই সময়কার প্রায় সব বৈষ্ণব কবিই পশ্চিমবঙ্গের তথা প্রেসিডেন্সী ও বর্ধমান বিভাগের।
কিন্তু একরকম আকস্মিকভাবে আমরা ষোলো শতকের শেষ পাদে আরাকান রাজ্যভুক্ত চট্টগ্রামে এবং সতেরো শতকের শেষার্ধে ও আঠারো শতকে মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত চট্টগ্রামে হিন্দু মুসলিম বহু পদকার পাচ্ছি। এই স্থানিক জনপ্রিয়তার ঋজু কারণ দুর্লক্ষ্য। এ কী চৈতন্য পার্ষদ চট্টগ্রামবাসী পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, মুকুন্দ ও বাসুদেব দত্তের প্রভাবের ফল!
.
০৫.
আমরা দেখছি, রাষ্ট্রিক বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে চট্টগ্রাম বাংলা দেশের তথা উত্তরভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রক্ষা করে চলেছিল। মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যে মুসলমানের রচনা বলতে প্রায় সবটাই তো চট্টগ্রামেরই দান। এমনকি বাঙলা দেশের যে-কোনো অঞ্চলের হিন্দুর চাইতে চট্টগ্রামের হিন্দুর দানও কম নয়। হয়তো আন্তর্জাতিক বন্দর এলাকার লোক বলেই সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যুগের আহ্বানে তারা সহজেই সাড়া দিতে পেরেছিল।
মধ্যযুগের চট্টগ্রামী হিন্দু কবিদের মধ্যে ষোলো শতকে পাচ্ছি কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্ৰীকরনন্দীকে। এরাই বাঙলায় মহাভারতের প্রথম অনুবাদক! সতেরো শতকে পাচ্ছি মৃগলুব্ধ প্রভৃতি রচয়িতা দ্বিজ রতিদেবকে ও লক্ষ্মণ দ্বিগ্বিজয়ের কবি দ্বিজ ভবানীনাথকে। আর আঠারো শতকে পাই সারদা-মঙ্গল প্রণেতা মুক্তারাম সেন, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী মাহাত্ম্য লেখক ব্রজলাল সেন (ইনি মুক্তারামের ভাই), কালিকামঙ্গল রচক নিধিরাম আচার্য ও গোবিন্দ দাস, মনসার ভাসান প্রণেতা রামজীবন বিদ্যাভূষণ, মৃগলুব্ধ সংবাদ রচক রামরাজা, গোকুল মঙ্গল লেখক ভক্তরাম দাস, সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচক ফকির চাঁদ প্রভৃতি ছাড়াও শঙ্কর দাস, শঙ্কর ভট্ট, বলরামদেব, রামতনু আচার্য, সদানন্দ ভট্ট প্রভৃতিকে।
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে আঠারো শতক থেকে বাঙালি হিন্দুরা প্রণয়োপাখ্যান রচনা শুরু করেন। এবং চন্দ্রাবলী রচয়িতা দ্বিজ পশুপতি ব্যতীত সবাই চট্টগ্রামবাসী। কাজেই এক্ষেত্রে পথিকৃতের গৌরব এঁদেরই। আজ অবধি আমরা আঠারো শতকের রামজীবন দাসের শশিচন্দ্রের উপাখ্যান, সুশীল মিশ্রের রূপবতী রূপবান উপাখ্যান, রাণীরাম দাসের শীত-বসন্ত, গোপীনাথ দাসের মনোহর মধুমালতী এবং উনিশ শতকের কবি মহেশচন্দ্র দাস চৌধুরীর সয়ফুল মুলুক জরুখভান পেয়েছি।
.
০৬.
চট্টগ্রামে প্রাপ্ত হিন্দুকবির পদগুলোর বৰ্হিরূপ বৈষ্ণব পদাবলীর মতো হলেও অনেক পদেই বৈষ্ণবীয় ভাব-সত্যের অভাব লক্ষণীয়। এমনকি ভণিতাগুলোও অনেক ক্ষেত্রে মহাজন পদাবলী সুলভ নয়, বরং মুসলিম রচিত পদের মতোই। এ-ও হয়তো আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতার ফল। মধ্যযুগে আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতা বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার সর্বাঞ্চলিক বিকাশের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এজন্যে চণ্ডী মঙ্গল ও ধর্ম মঙ্গলের উদ্ভব ও বিকাশ কেবল রাঢ় অঞ্চলেই নিবদ্ধ দেখি। আবার পূর্ববঙ্গেই যেন মনসা কাহিনীর জনপ্রিয়তা ছিল সর্বাধিক। বৈষ্ণব সাহিত্যের উদ্ভব এবং বিকাশও সীমিত দেখি পশ্চিমবঙ্গে এবং আধুনিক চট্টগ্রাম বিভাগে (সিলেট ব্যতীত) বাউল সম্প্রদায় চিরকালই অনুপস্থিত। এখানে সত্যপীরের প্রভাবও ছিল সামান্য।
এমনকি বহুকাল ধরে মুসলমানদের বাঙলা সাহিত্য চর্চাও বিশেষ করে নিবদ্ধ ছিল চট্টগ্রামে ও রোসাঙ্গে। তেমনি দোভাষী রীতির ও পুঁথিসাহিত্যের উন্মেষ ও বিকাশ এবং কবিওয়ালাদের আবির্ভাব সীমিত ছিল পশ্চিমবঙ্গের এখানকার প্রেসিডেন্সী বিভাগে। আবার দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গেই বিশেষ চর্চা হয়েছিল লৌকিক উপদেবতা ও পীরকাহিনীর, এবং গাথা-গীতিকা রচিত হয়েছে বিশেষ করে ময়মনসিংহে ও চট্টগ্রামে।
অতএব, মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের একটা সর্ববঙ্গীয় চরিত্র ও রূপের অনুধ্যানে যতই আমরা আনন্দিত হতে চাই এবং অখণ্ডতা ও ঐক্যবোধের আগ্রহে যতই কেন সামগ্রিক রূপ-কল্পনাকে প্রশ্রয় দিই, ভৌগোলিক দূরত্ব যে বিভিন্ন অঞ্চলের বাঙলাভাষীদের পারস্পরিক মানসযোগ রক্ষার অন্তরায় ছিল, তা অস্বীকার করা যাবে না।
বাউল তত্ত্ব
০১.
মৈথুনতত্ত্ব ও টোটেম-বিশ্বাস অতি প্রাচীন। দুনিয়ার তাবৎ জাতির আদিম বিশ্বাস ও জীবনচর্যার সঙ্গে এ দুটো জড়িত। টোটেম-বিশ্বাসের একটি পরিচায়ক হচ্ছে পশু-পাখির নামানুসারে গোত্র ও ব্যক্তির নাম গ্রহণ। এটি আমরা প্রাচীন ভারতে যেমন দেখি, তেমনি অস্ট্রেলিয়া-আমেরিকার আদিবাসীদের মধ্যেও পাই। মৈথুনতত্ত্ব ভিত্তি করে শাস্ত্র ও দর্শন গড়ে ওঠে প্রধানত কৃষিজীবী সমাজেই–বিদ্বানদের মত এই। তার কারণ মৈথুন ও প্রজনন প্রাচীনকালের চেতনা অনুসারে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ছিল।২ এবং ধন উৎপাদন পদ্ধতির অভিন্নতর ধারণা থেকেই মৈথুনতত্ত্ব ধর্মশাস্ত্রের মর্যাদায় উন্নীত হয়। এই জন্যে মৈথুন-ক্রিয়া ও উৎসবের সঙ্গে ফসলের সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ। জাভা, নিউগিনি, অস্ট্রেলিয়া, মেক্সিকো প্রভৃতি আদিবসী অঞ্চলে এবং ভারতের আদিবাসী সাঁওতাল, হো, মুণ্ডা, পাঞ্চা, কোটার প্রভৃতির মধ্যে আজো মৈথুন উৎসব বিদ্যমান। এ হচ্ছে ফসল প্রাপ্তির বাঞ্ছায় সিদ্ধির আবহ সৃষ্টির প্রয়াস। আমাদের দেশে চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে আজো অনাবৃষ্টির সময়ে ছেলেমেয়েরা কুলো নিয়ে ঘরে ঘরে পানি মাগে। তখন যেসব ছড়া আওড়ায় তাতে আছে কলাতলে এক গলা পানি, বৌ নাইয়রের নৌকা আনি ইত্যাদি। এতে বোঝা যায়, প্রবল বারিপাত জাত পরিবেশটা এরা কল্পনা করে, এবং তা-ই উচ্চারিত হয় বৃষ্টির আগমনী গানে। শস্য উৎপাদনের সঙ্গে মৈথুনের এমনি প্রতীকী আবহ সৃষ্টির সম্পর্ক রয়েছে। R. Briffault তাই বলেন :
The assimilation of the fruit-bearing soil to the child-bearing women is universal ….. the fecundity of the earth and the fecundity of women are viewed as being one and the same quality.
James Frazer-ও বলেন :
In the opinion of those who performed them (ceremonies) the marriage of trees and plants could not be fertile without the real union of the human sexes …. ruder races in other parts of the world have consciously employed the intercourse of the sexes as a means to ensure the fruitfulness of the earth; and some rites which are still of were till lately, kept up in Europe can be reasonably explained only as stunted relics of similar practice.
G. Thomson-ও বলেন :
The desired reality is described as though already present.
এ বিশ্বাসের আরো একটি দিক রয়েছে। পৃথিবীর পিছিয়ে পড়া মানুষদের মধ্যে আজো এ বিশ্বাস টিকে আছে যে, নারীদেহ থেকেই আদি শস্যের উদগম হয়েছে। আমাদের দেশেও এ বিশ্বাস চালু ছিল তার প্রমাণ রয়েছে মার্কেন্ডেয় পুরাণে, আর আভাস আছে অনেক ক্ষেত্রে। মার্কেন্ডেয় পুরাণে দেবী বলেছেন :
ততোহহম খিলং লোকমাত্মদেহসমুদ্ভবৈ:।
ভবিষ্যামি সুরা: শাকৈরাবৃষ্টৈ: প্রাণধারকৈ: ॥
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতিং তদাস্যাম্যহং ভূবি।
[অনন্তর আমি নিজদেহ উদ্ভুত প্রাণধারক শাকের সাহায্যে যত দিন না বৃষ্টি হয়, ততদিন জগৎ পালন করব। এইজন্য আমি শাকম্ভরী নামে বিখ্যাত হব ] এই শাকম্ভরীই দুর্গা। দুর্গোৎসব হয় শরৎকালে। এতে সেই শস্যদেবীর পূজা উৎসবের আভাস মেলে। দুর্গাপূজার ভিতরেই দেখিতে পাই ….. একটি কলাগাছের সহিত কচু, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিন্দু, ডালিম, মানকচু, অশোক এবং ধান্য একত্রে যে শস্যবধূ নির্মাণ করা হয়, …. এই শস্যবধূকেই দেবীর প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করিয়া প্রথমে পূজা করিতে হয়। শাকম্ভরী বলেই দুর্গা অন্নদা-অন্নপূর্ণা রূপেও পরিচিতা। হরপ্পায় আবিষ্কৃত একটি সীলে দেখা যায় একটি নগ্ন নারীমূর্তির দুটো পা দুপাশে ছড়ানো আর তার যোনি থেকে একটি লতা বেরিয়ে এসেছে। এ নারী যে শস্যদেবী এবং ফসল যে এদেবীর আত্মদেহসমুদ্ভবৈ : তাতে সন্দেহ নেই। এদেশের উমা ও প্রাচীন আনার্যদেবী; কেবল তাই নয়, এর বহির্ভারতিক অস্তিত্বও দেখা যায় :
The babylonian word for mother is Ummu or Umma, the Accadian Ummi and the Dravidian is Umma. These words can be connected with each other and with Uma the mother goddess.
কৃষির শুরু নারীদের হাতেই। প্রসবিনী নারীরা হয়তো নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে ফসলি উৎপাদনী ভূমির প্রজননক্রিয়া কল্পনা করেছে। তা থেকেই মৈথুন-প্রজননে এবং প্রসব উৎপাদনেও অভিন্ন পদ্ধতি কল্পিত হয়েছে। R. Briffault বলেন :
The art of cultivation has developed exclusively in the hands of women.
G. Thomson 76901 :
Food-gathering led to the cultivation of seed in plots adjacent to the settlement and so garden tillage is womens work.
অন্যান্য বিদ্বানেরাও এ মত সমর্থন করেন। পিতৃপ্রাধান্য অর্থে বীজ প্রাধান্য, আর মাতৃপ্রাধান্যসূচক ক্ষেত্র প্রাধান্য–শব্দদুটোর অভিধার মধ্যেও কৃষিপদ্ধতির আভাস রয়েছে। নারী উদ্ভাবিত কৃষিপদ্ধতির সঙ্গে নারীদেবীর যোগ থাকাই স্বাভাবিক। তাই পৃথিবীর সর্বত্র বসুমাতার কল্পনা প্রশ্রয় পেয়েছিল। পশুজীবী আর্যেরা এদেশে এসে কৃষিজীবী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষি সংক্রান্ত ও কৃষিজীবী সমাজের সংস্কারের প্রভাবে পড়েছিল বলে অনুমান করি। তাই বাজসনেয়ী সংহিতা, ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য প্রভৃতিতে মৈথুন, প্রজনন, জীবন ও সম্পদ প্রভৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বীকৃত হয়েছে।১৭ ছান্দোগ্যে আছে :
ক. হে গৌতম, স্ত্রীলোকই হলো যজ্ঞীয় অগ্নি, তার উপস্থই হলো সমিধ। ওই আহ্বানই হলো ধূম। যোনিই হলো অগ্নিশিখা। প্রবেশক্রিয়াই হলো অঙ্গার। রতি সম্ভোগই হলো স্ফুলিঙ্গ।
অগ্নিতে দেবতারা রেতর আহুতি দেন। সেই আহুতি থেকেই গর্ভ সম্ভব হয়।
খ. ছান্দোগ্যের বামদেব্য ব্রতকথায় আছে।
যে একইভাবে বামদেব্য সামকে মৈথুনে প্রতিষ্ঠিত জানে; সে মৈথুনে মিলিত হয়। (তার) মিথুন থেকে সন্তান উৎপন্ন হয়। সে পূর্ণজীবী হয়; সন্তান, পশু ও কীর্তিতে মহান হয়। কোনো স্ত্রীলোককেই পরিহার করবে না–এই-ই ব্রত।
এসব আদিম ধারণা থেকেই উদ্ভূত আদিম আচার আজো নতুন তাৎপর্যে ধর্মশাস্ত্রের অঙ্গ হয়ে আছে। আজো তাই লতা, স্ত্রীভগ, যন্ত্র প্রভৃতি সাধন-পূজনের অপরিহার্য অঙ্গ। কেবল এখানেই শেষ নয়, দেবতার হাতের ডালিম হচ্ছে রক্ত তথা রজ : ঋতুর প্রতীক। রজ: আবার সিন্দুরেও প্রতীকীরূপ নিয়েছে। আর পদ্ম হচ্ছে নারীযোনির প্রতীক।
উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে চেয়েছি যে আর্যেরা প্রাকৃতিক শক্তির পূজারী ছিল। পশুজীবী আর্যরা প্রকৃতি-প্রতীক দেবতা বায়ু, বরুণ, অগ্নি, ইন্দ্র প্রভৃতি কল্পনা করেছে। আর অনার্যেরা গুণময় শক্তির পূজারী ছিল। প্রকৃতির প্রসাদ নির্ভর আদিকালের অজ্ঞ অসহায় মানুষ কল্পনাশ্রয়ী না হয়েই পারেনি। অসহায় অসমর্থের অপ্রাপ্তি-অসাফল্যের ভয় থেকেই বিশ্বাস উৎসারিত। আজো দুর্বলচিত্তে তুকতাক ও শুভাশুভ প্রতাঁকের প্রভাব অপরিমেয়। নিজের মনোবাঞ্ছা সিদ্ধির অনুকূল পরিবেশ পেলে যে-কোনো মানুষ তার প্রয়াসে ও বাঞ্ছায় সিদ্ধি সম্বন্ধে আশান্বিত হয়ে ওঠে। বাহ্য নিদর্শন ঘিরে এই যে সিদ্ধির বা অসিদ্ধির কল্পনার প্রশ্রয় তা আজো কম নয়। তুকতাক, দারু-টোনা এবং শুভাশুভ প্রতীক, তিথি, নক্ষত্র ও দিনক্ষণের উপর কর্মের ফলাফল নির্ভরতায় বিশ্বাস আজো অধিকাংশ লোকের মনে দৃঢ়মূল। অক্ষম মানুষকে বাঞ্ছ সিদ্ধির কামনার তীব্রতাই যাদু বিশ্বাসের প্রবর্তনা দেয়। মনের এমনি অবস্থায় সিদ্ধির অনুকূল কাল্পনিক ও আচারিক আবহ সৃষ্টি করাও অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। দুনিয়ার মানুষের আদিম জীবন-জীবিকা সংস্থায়। স্বাভাবিকভাবেই তাই এ মনোবল সঞ্চয়ের সহায় যাদুবিশ্বাস চালু ছিল। প্রয়োজন ও ক্ষেত্র অনুসারে নানা বৈচিত্র্যে বিবর্তিত হয়ে আজকের দিনের সমাজে ও ধর্মে রূপ নিয়েছে।
কৃষিজীবী অনার্যেরা দুনিয়ার আর আর আদিম কৃষিজীবীর মতো মৈথুন তত্ত্বকেই প্রাধান্য দিয়েছিল। নারী-উদ্ভাবিত কৃষি-পদ্ধতিতে ভূমির ফসল উৎপাদন নারীর সন্তানধারণের অনুরূপ বলে কল্পিত হয়েছে। এ বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা থেকেই জগৎ-সৃষ্টিতেও তারা প্রকৃতি ও পুরুষের–নর ও নারী স্বরূপার মৈথুনতত্ত্বে আস্থা রেখেছে। মনোবল সঞ্চয় ও বাঞ্ছসিদ্ধির সহায়ক আবহ সৃষ্টির প্রয়োজনে তারা মৈথুনকে বীজ বোনার শুভযোগ সৃষ্টির প্রারম্ভানুষ্ঠানরূপে গ্রহণ করে। পরে সমাজ ব্যবস্থার ও উৎপাদন পদ্ধতির বিবর্তন হয়েছে এবং আদিম সংস্কারও নানা তাত্ত্বিক চিন্তাযযাগে কলেবরে পুষ্ট হয়েছে। কালিক ব্যবধানে আদি উদ্দেশ্যের বিস্মৃতি ঘটেছে এবং উন্নততর মননের দ্বারা নতুন ও জটিলতর তত্ত্ব ও উদ্দেশ্য আরোপিত হয়েছে। বসুমতী বা শস্যদেবীরূপে যেই মানস প্রসূতার প্রথম আবির্ভাব, তিনি আদ্যাশক্তি। তার থেকেই পরম-পুরুষের উৎপত্তি। শক্তিস্বরূপা নারীর সঙ্গে অবিনাবদ্ধ হয়ে পুরুষ হয় শক্তিমান। শক্তি ও শক্তিমান তাত্ত্বিক কল্পনায় একসময় অদ্বয়, অভিন্ন বা অদ্বৈত সত্তারূপেও কল্পিত হয়, আবার দ্বৈতরূপেও তার প্রকাশ-সম্ভাবনা অস্বীকৃত হয়নি। ফলে মায়া-ব্রহ্ম, শিব-শিবানী, পুরুষ-প্রকৃতি, বিষ্ণু-লক্ষ্মী প্রভৃতি আদ্যশক্তিরূপে কল্পিত হয়েছে। এখানেও সৃষ্টি-সহ মৈথুনতত্ত্ব স্বীকৃত। মৈথুন মাধ্যমে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা এই নারী-পুরুষ তত্ত্ব-ভাবনায় তথা মিলন-তত্ত্ব কল্পনায় প্রচুর প্রেরণা দিয়েছে। কিন্তু কালে মৈথুনতত্ত্বের আদি উদ্দেশ্যের বিস্তৃতি ঘটেছে এবং নতুন তাৎপর্য পেয়ে অধ্যাত্ম-মাধুর্যে মহৎ এবং তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতায় অসামান্য হয়ে উঠেছে। এর বিচিত্র প্রকাশ আমরা সাংখ্যে, যোগে, তন্ত্রে ও শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব গাণপত্যে-লিঙ্গায়েতে দেখছি। তবু এর আদিরূপের রেশ রয়েছে জয়পুর, পাঞ্জাব, নিলগিরি, ছোটনাগপুর, এবং উত্তর ও উত্তর-পূর্ব বাঙলার আদিবাসীদের মধ্যে। মৈথুন যেমন আদিতে ফসল উৎপাদনের আনুষ্ঠানিক অঙ্গরূপে বিবেচিত হয়েছে, তেমনি আবার রতিনিরোধ সাধনায়ও প্রবর্তনা দিয়েছে। পৃথিবীর নানা অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে তারও পরিচয় রয়েছে। J. Frazer বলেছেন :
Either he may infer that by yielding to his appetites he will thereby assist in the multiplication of plants and animals; or he may imagine that the vigour that he refuses to extend in reproducing his own kind, will form as it were a store of energy whereby other creatures, whether vegetable or animal, will somehow benefit in propagating their species. Thus from the same crude philosophy, the same primitive notions of nature and life, the savage may derive by different channels a rule either of profligacy or of asceticism.
কাজেই বামাচারী ও কামবর্জিত সাধনার উৎস অভিন্ন হতে বাধা নেই।
.
০২.
সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র যে অনার্য-মানস উদ্ভূত আদিম মত ও আচার-আজকাল এ- কথা আর অস্বীকৃত হয় না। বাঙলা দেশ মূলত-আর্য অধ্যুষিত দেশ নয়, এদেশে আর্য-অনুপ্রবেশ বেশি হয়নি। গুপ্ত ও সেন আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের কিছুটা প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখা দেয়, আর পাল শাসনে বৌদ্ধধর্ম রাজধর্ম হয়। কাজেই এদেশে অবিমিশ্র আর্য প্রভাব কোনদিন পড়েনি। বেলভেলকার ও রানাডে বলেন, যোগ আদিতে অবৈদিক সাধন পদ্ধতি ছিল। এবং এর সঙ্গে আদি যাদুবিশ্বাসের সম্পর্কও তাঁরা অস্বীকার করেননি। বলেছেন, Sympathetic magic-এর ধারণাও এর মূলে রয়েছে। A.E. Gough ও বলেন–স্থানীয় অনার্য আদিবাসীদের কাছ থেকেই বৈদিক আর্যরা কালক্রমে যোগ সাধন-পদ্ধতিটা গ্রহণ করেছিল। H.H. Zimmer বলেন, সাংখ্যের তত্ত্বগুলি বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের অন্তর্গত নয়। দুইটি ধ্যান-ধারণা স্বতন্ত্র। সাংখ্য ও যোগ জৈনদের যান্ত্রিক দর্শনের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। সাংখ্য ও যোগের মূল ধারণাগুলি অত্যন্ত প্রাচীন ও বেদপূর্বযুগের। পাঁচকড়ি বানার্জী বলেন, তন্ত্র অতি প্রাচীন, তন্ত্র ধর্মই বাঙলার আদিম ধর্ম এবং ইহা অবৈদিক ও অনার্য। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, কৌটিল্য তিনটি মাত্র দর্শনের উল্লেখ করেন–সাংখ্য, যোগ ও লোকায়ত। সাংখ্যমত সকলের চেয়ে পুরান, উহা মানুষের করা এবং পূর্বদেশের মানুষের করা। উহা বৈদিক আর্যদের মতো নহে; বঙ্গ, বগধ ও চের জাতির কোনো আদি বিদ্বানের মতো। বৌদ্ধমত সাংখ্যমত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, এ কথা অশ্বঘোষ একপ্রকার বলিয়াই গিয়াছেন। বুদ্ধদেবের গুরু আড়ার কলম ও উদ্ৰক–দুজনই সাংখ্য মতাবলম্বী ছিলেন। শশিভূষণ দাশগুপ্তও তন্ত্রকে আদিম অনার্য গুপ্তশাস্ত্র বলেছেন।
এসব মতের ধারকেরা ব্রাহ্মণ্যবাদী, জৈন ও বৌদ্ধদের কাছে লোকায়তিক বলে পরিচিত ছিল; যদিও বেদাদি সব শাস্ত্রগ্রন্থেই আমরা এসব মতের প্রভাব লক্ষ্য করি। তার কারণও আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, তার সঙ্গে এও স্মর্তব্য যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অনার্যের আচার-সংস্কারের প্রতি সামাজিক রাজনৈতিক কারণেও উদাসীন বা শ্রদ্ধাহীন থাকা আর্যদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তন্ত্র সম্বন্ধে শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন :
Tantrism is neither Buddhist nor Hindu in origin, it seems to be a religious under-current, originally independent of any obstruse metaphysical speculation flowing on from an obscure point of time in the religious history of Inida, with these practices and yogic processes, which characterise Tantrism as a whole, different philosophical, or rather theological systems got closely associated in different times …. these esoteric practices (yogic) when associated with the theological speculations of the saivas and saktas, have given rise to Saiva and Sakta Tantrism, when associated with the Buddhistic speculations have given rise to the composite religious system of Buddhist Tantrism, and again, when associated with the speculations of Bengal Vainavism the same esoteric practices have been responsible for the growth of the esoteric Vaisnavite Cult, known as the Vaisnava Sahajia movement.
তিনি আরো বলেন, বৃহত্তর ভারতে এই তান্ত্রিকতার একটি বিশেষ ভূমি ভাগ আছে। উত্তর পশ্চিম কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া নেপাল, তিব্বত, ভূটান, কামরূপ এবং বাঙলাদেশ–হিমালয় পর্বত সংশ্লিষ্ট এই ভূভাগকেই বোধহয় বিশেষভাবে তান্ত্রিক অঞ্চল বলা চলে। হিমালয় সংশ্লিষ্ট এই বিস্তৃত অঞ্চলটিই কী তন্ত্র বর্ণিত চীন দেশ বা মহাচীন? তন্ত্রাচার চীনাচার নামে সুপ্রসিদ্ধ; বশিষ্ট চীন ও মহাচীন হইতে এই তন্ত্রাচার লাভ করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রসিদ্ধিও সুপ্রচলিত। এই সকল কিংবদন্তিও আমাদের অনুমানের পরিপোষক বলিয়া মনে হয়। আমরা লক্ষ্য করিতে পারি, প্রাচীন তন্ত্র অনেকগুলিই কাশ্মীরে রচিত। ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও কিছু কিছু তন্ত্র রচিত হইলেও বঙ্গকামরূপ মুখ্যভাবে পরবর্তী তন্ত্রের রচনা স্থান–নেপাল-ভুটান-তিব্বত-অঞ্চলে এগুলির বহুল প্রচার এবং অদ্যাবধি সংরক্ষণ।…. তন্ত্রোক্ত দেহস্থ ষটচক্রের …. অধিষ্টাত্রী দেবী হইলেন ডাকিনী, রাকিনী, লাকিনী, শাকিনী এবং হাকিনী।…. এই ডাকিনী দেবী কোনো নিগূঢ় জ্ঞানসম্পন্না তিব্বতী দেবী হইবেন। … ভূটানে লাকিনী ও হাকিনী দেবীর সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেন, তিন্ত্র, যোগ, সাংখ্য প্রভৃতির মূলে আছে কৃষিকেন্দ্রিক জাদু বিশ্বাস এবং জাদু অনুষ্ঠান। তাঁর মতে তন্ত্র শব্দটিও সন্তান উৎপাদন সম্পর্কীয়।
সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র মূলত দেহাত্মবাদী ও নাস্তিক মত। যোগে ও তন্ত্রে পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে ঈশ্বর স্বীকৃত হলেও, এসব সাধনায় ঈশ্বরোপাসনার স্থান অপ্রধান। দেহতত্ত্বই মুখ্য। এই দেহাত্মবাদী নাস্তিক মতকে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা গোড়ার দিকে অসুর-মত বলে আখ্যাত করেছেন। গীতায় বলা হয়েছে অসুর মতে অপরস্পর সম্ভুত কিমন্যং কামহৈতুকম অর্থাৎ জগৎ নারী-পুরুষের মিলনজাত এবং কামোদ্ভূত। ১৬৮। একে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা লোকায়ত বলে অবজ্ঞা করেছেন। সাধারণত মাধবাচার্যের সর্বদর্শন সংগ্রহ, শঙ্করাচার্যের (?) সর্বসিদ্ধান্ত সংগ্রহ, হরিভদ্রসূরীর ষড়দর্শন সমুচ্চয়, কৃষ্ণ মিত্রের প্রবোধচন্দ্রিকা নাটক, ভাগবত, বৃহদারণ্যক, গীতা, বিষ্ণু পুরাণ, মনুসংহিতা, এবং বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদির আলোকে লোকায়ত তত্ত্ব নিরূপণের চেষ্টা হয়। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীদের এসব গ্রন্থ থেকে মতবাদটির স্বরূপ প্রকাশিত হয় না। আসলে আদিম তান্ত্রিক, যোগী এবং সাংখ্য মতবাদীরাই লোকায়তিক। তাই শীলাঙ্ক রচিত সূত্র-কৃতাঙ্গ সূত্রের ভাষ্যে সাংখ্য ও লোকায়তিকে বিশেষ পার্থক্য স্বীকৃত হয়নি। তিন মতই মূলে এক এবং এমনকি গীতার আমলেও যোগ ও সাংখ্য অভিন্ন ছিল। সাংখ্য হচ্ছে তত্ত্ব আর যোগ হচ্ছে সাধনশাস্ত্র। সাংখ্য এবং তন্ত্রের সম্পর্কও তাই। পরবর্তীকালে যোগ ও তন্ত্র দুটো ভিন্ন ধারায় যেমন চলেছে, তেমনি আবার যোগতান্ত্রিক মিশ্ৰধারাও সৃষ্টি করেছে। এতে শৈব-শাক্ত-বৌদ্ধ-জৈন তান্ত্রিক সম্প্রদায় যেমন পেয়েছি, তেমনি কামাচার বর্জিত বিশুদ্ধ যোগী সম্প্রদায়েরও উদ্ভব দেখি। এসব মত কালে বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্যবাদের শাখা ও উপমত রূপে গৃহীত হয়েছে। এবং জৈন ও বৌদ্ধ মতের অন্তর্গত হয়েও এগুলো মর্যাদা পেয়েছে। তারই জের রয়েছে বৈষ্ণব সহজিয়া, সহজিয়া, নাথ প্রভৃতি বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য-ঘেঁষা সম্প্রদায়ে আর অবলুপ্ত রেশ রয়েছে সাওতাল, হো, পাঞ্চা, কোটার প্রভৃতির সমাজে।
.
০৩.
আদিতে হিন্দু সিন্ধুবাসী অর্থে প্রযুক্ত হলেও কালে গোটা উপমহাদেশ হিন্দুস্তান এবং জাতি ও ধর্মসম্প্রদায় হিসেবে দেশের সব অধিবাসী হিন্দু নামে পরিচিত হতে থাকে। এভাবে আর্য-অনার্য বহু উপধর্মে ও মতে আস্থাবান এক বিপুল মনুষ্য-সমাজ হিন্দু–এই সাধারণ নামে অভিহত হয়। অতএব হিন্দু বললে কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্মমতবাদীকে বুঝায় না। তারা জাতি অর্থে অভিন্ন হলেও ধর্মসম্প্রদায় হিসেবে বহুধা বিভক্ত। অন্যান্য দেশে কোনো ধর্মমতে দীক্ষিত জনসমষ্টি ধর্মের বা ধর্মপ্রবর্তকের নামে পরিচিত হয়; যেমন মুসলিম, খ্রীস্টান, কনফুসিয়ান, জোরাস্টীয়ান প্রভৃতি। বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কোনো একজনের প্রবর্তিত ধর্ম নয় বলেই হিন্দু নামের এমন ব্যাপক ও দ্ব্যর্থক ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারা অনুসরণ করেই এই ধর্মের উন্মেষ, বিকাশ ও বিচিত্র রূপান্তর ঘটেছে। তাই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও তার প্রশাখাগুলোকে অবশ্যম্ভাবী ঐতিহাসিক বিকাশও বলা চলে। আধুনিক সমাজতত্ত্বে এই বিবর্তনের গুরুত্ব অনেকখানি। তাই W.W. Hunter বলেছেন :
India thus forms a great Museum of races, in which we can study man from his lowest to his highest stages of culture. The Specimens are not fossils or dry bones, but living communities. :
এখানে সত্যই Fragments of a Pre-historic world কিংবা remnants to our own day of the stone age calcule
হিন্দুর উপমতগুলোর বাহ্যত এক-একজন প্রবর্তক থাকলেও আসলে বিভিন্ন মতের মিশ্রণে গড়ে-উঠা প্রবল আঞ্চলিক মতবাদের তারা প্রচারক মাত্র। কেননা, এগুলো মূলত ইষ্টদেবতার প্রাধান্য এবং লক্ষ্যের বৈশিষ্ট্যজাত উপমতই। এগুলাকে বলা যায়–বৈদিক মতের প্রশাখা। এখানে উল্লেখ যে ঋগ্বেদেও কোনো একক মত প্রতিষ্ঠার প্রয়াস নেই। বিস্তৃত কালিক পরিসরে বিভিন্ন কবি রচিত সূক্তসমষ্টিই ঋগ্বেদ বা ঋক্-সংহিতা। এ জন্যে কোনো কোনো মতাদর্শের প্রাধান্য থাকলেও ঋগ্বেদে পরবর্তী প্রায় সব মতেরই কিছু কিছু সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন তারাপদ চৌধুরী বলেন :
যে সকল ভক্তিমার্গে পরব্রহ্মেরই প্রকাশরূপে কোনো ইষ্ট দেবতার কল্পনা করা হইয়াছে। এবং ভক্তির কোমলতা এবং ভক্তের কঠোর নৈতিক আচরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে, তাহাদের সূচনা বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন রীতির তপশ্চর্যা, এমনকি তান্ত্রিক আচারগুলির পূর্বাভাস বেদে বর্তমান। বেদান্তের অদ্বৈতবাদ এবং মায়া সম্বন্ধে ও জ্ঞানের মাধ্যমে মোক্ষ লাভ সম্বন্ধে ইঙ্গিত, মীমাংসা মতানুযায়ী যজ্ঞের সর্বশক্তিমত্তা, সাংখ্য দর্শন সম্মত ত্রিগুণ এবং প্রকৃতির অন্ধ প্রবণতা, যোগদর্শন সম্মত ইন্দ্রিয় সংযম এবং চিত্তের অভিনিবেশ এবং ন্যায়-বৈশেষিক মতানুসারে ব্রহ্মপ্রাপ্তির জন্য যথার্থ বৌদ্ধিক দৃষ্টি ও যথার্থ বাক্যের প্রয়োজনীয়তা–এই সকলেরই পূর্বাভাস বেদে দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত আত্মা, মন, পরব্রহ্ম, বিশ্বের অভিব্যক্তি, কর্ম, পুনর্জন্ম এবং মোক্ষ প্রভৃতি সম্বন্ধে সাধারণ সমস্যাগুলির আলোচনাও আছে। পরবর্তীকালে বেদগুলিকে যে যাবতীয় ধর্ম ও দর্শনের প্রধান উৎস বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছিল, তাহাতে আশ্চর্যের বিষয় কিছু নাই।
তেমনি পরবর্তীকালের মহাভারতে তথা গীতায়ও নানা মতের অসমন্বিত মিশ্রণ ঘটেছে। অতএব সব কয়টি মত ও উপমতের উদ্ভবের ইতিহাস অত্যন্ত জটিল এবং দুর্নিরীক্ষ্য ও দুর্নির্ণেয়। দেশী-বিদেশীর, শাসক-শাসিতের এবং আর্য-অনার্যের নানা ধারণা, সংস্কার, আচার, আদর্শ ও লক্ষ্যের বিচিত্র মিশ্রণে ও সমাবেশে–কখনো সমন্বয়ে, কখনো বা অজ্ঞতাপ্রসূত বিকৃত-প্রভাবে সব শাখা ও উপশাখাগুলো গড়ে উঠেছে। তাই নিশ্চিত বিশ্বাসে কিংবা যুক্তি ও তথ্য প্রয়োগে কোনো নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। শেষ অবধি বিদ্বানে বিদ্বানে মতানৈক্য থেকেই যায়। অবশ্য যতই আলোচনা হচ্ছে, জটিলতাও ততই হ্রাস পেয়ে গবেষণার পথ খুলে দিচ্ছে।
সাম্প্রতিক গবেষণায় বোঝা যাচ্ছে বৈদিক বিধি-বিধান এবং ভাবকল্প একান্তভাবে আর্য নয়। পশুজীবী আর্যেরা মূলত প্রাকৃত শক্তির পূজারী এবং কর্ম ও কর্মফলে আস্থাবান। কিন্তু কৃষিজীবী অনার্য গোষ্ঠীরা তাদের জীবিকার গরজেই ভাববাদী ও প্রতীকপ্রিয় না হয়ে পারেনি।
অনুমান করি, উর্বরা ভারতভূমির অনিঃশেষ চারণক্ষেত্র আর্যদের স্থায়ী বসবাসে প্রলুব্ধ করে, আর অনায়াসলভ্য ফলমূল তাদেরকে জীবিকার ভাবনা-মুক্তির আশ্বাস দিয়ে কৃষিকার্যে প্রবর্তনা দেয়। এভাবে এ নতুন দেশে নতুন জীবিকার মাধ্যমে আর্যরা কৃষি সম্পর্কিত আচার-সংস্কারেও গোড়া থেকেই প্রভাবিত হতে থাকে। এই প্রভাবেরই স্বাক্ষর রয়েছে হয়তো বেদের বিভিন্ন মণ্ডলের নারী, অদ্বৈততত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব ও ভাব প্রতীকী কল্পনার মধ্যে–যা সাধারণভাবে আর্য মননের লক্ষণ বলে ব্যাখ্যা করা চলে না। বেদে-ব্রাহ্মণে-উপনিষদে যা আছে সবই আর্যমানসজাত, এ ধারণা তাই যৌক্তিক আলোচনা ও সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। সি. কুহ্বান রাজা বলেছেন–সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা এবং দ্রাবিড়ভ্যতার প্রভাবেই–১. সর্বসাধারণের জীবনে অরণ্যের প্রভাব, ২. মন্দিরে উপাসনা ও তার সঙ্গে অধিকতর মূর্ত আকারে দেবতার অনুধ্যান, ৩. বিশ্বজগতের পরিকল্পনা ধারার মধ্যে পশু, পক্ষী, বৃক্ষ প্রভৃতির উচ্চস্থান লাভ, ৪. ঐশী-শক্তির স্ত্রীরূপকে উচ্চতর মর্যাদা দান, ৫. ঈশ্বরের স্রষ্টত্ব এবং ৬. জাতীয় মহাপুরুষ হিসাবে দেবতাদের আবির্ভাব এবং মানুষের দেবত্বে উন্নয়ন। তার মতে সাংখ্য মত অবৈদিক। ভক্তির বিকাশও অবৈদিক প্রভাবজ। বেদান্ত ও ভক্তিবাদের মাধ্যমে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনজ্জীবনও ঘটে প্রধানত দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় দিয়ে। কুমারিল ভট্ট অন্ধদেশের লোক, শঙ্করাচার্যের জন্মস্থান কেরলা, রামানুজ তামিল দেশে আর মাধবাচার্য কর্ণাট দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এবং বিষ্ণু আর শিবের শক্তিমহিমা ও ক্রিয়ার ধারণাও অবৈদিক। তাই আগম। শাস্ত্রও অবৈদিক।–
তারাপদ চৌধুরীও বলেন, বৈদিক ধর্মবিশ্বাসের পাশাপাশি মন্ত্রতন্ত্র, বশীকরণ এবং ইন্দ্রজালের ক্ষমতা সম্বন্ধে সাধারণের যে ব্যাপক বিশ্বাস ছিল, তাহাও এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন। বৈদিক সাহিত্যে সর্বত্রই এ বিষয়গুলির ইতস্তত উল্লেখ আছে বটে, তথাপি বিশেষভাবে এইগুলি অথর্ববেদ এবং তাহার অনুষ্ঠানাঙ্গ কৌশিক-সূত্র উহাদের বিষয়। সেইজন্যই এই গ্রন্থ দুইটিতে পরবর্তী তন্ত্রশাস্ত্রের সূচনা রহিয়াছে। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেন :
It is now becoming more and more clear that the Non-Aryan contributed by far the greater portion in the fabric of Indian civilization, and a great deal of Indian religious and cultural traditions, of ancient legend and history, is just non-Aryan translated in terms of the Aryan speech ….. the ideas of Karma and transmigration, the practice of Yoga the religious and philosophical ideas centring round the conception of the divinity as Siva and Devi and as Vishnu, the Hindu ritual of Puja as opposed to the Vedic ritual of Homa–all these and much more in Hindu religion and thought would appear to be non-Aryan in origin, a great deal of Puranic and epic myth, legend and semi-history is Pre-Aryan, much of our material culture and social and other usages, eg. the cultivation of some of our most important plants like rice and some vegetables and fruits like tamarind and the coconut etc., the use of betel leaf in Hindu life and Hindu ritual, most of our popular religion, most of our folk crafts, our nautical crafts, our distinctive Hindu dress (The dhoti and sari), our marriage ritual in some parts of India with the use of Vermilion and turmeric and many other things would appear to be legacy from our Pre-Aryan ancestors.
এবার আমরা গুরুত্বপূর্ণ শাস্ত্রগ্রন্থ ও দর্শনগুলো অবলম্বন করে ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুসরণ করব।
উপনিষদ
উপনিষদগুলোতে সমাজ-স্বীকৃত বৈদিক মূলতত্ত্ব, দেবতা, যজ্ঞ ও অন্যান্য আচার-বিরোধিতা লক্ষণীয়। এ ব্যাপারে বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য-প্রাচীন বলে স্বীকৃত এ দুটো উপনিষদের বক্তব্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
বৃহদারণ্যকে আছে –যে ব্যক্তি আত্মা ব্যতীত অন্য কোনো দেবতার আরাধনা করে, সে দেবগণের গৃহপালিত পশুবিশেষ।
পরবর্তীকালে শঙ্করও যজ্ঞাদি আচার ও দেবপূজায় অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। বস্তুত আরণ্যক রচনাকাল থেকেই ক্রিয়াকাণ্ডে বিশ্বাসী আর্যেরা ভাববাদী হয়ে উঠল। তার ফলেই উপনিষদে যজ্ঞ ও দেবতাদির প্রতি বিরূপতা দেখা দেয়। এমনকি পরবর্তী উপনিষদ শ্বেতাশ্বতর প্রভৃতিতে যজ্ঞের মহিমা পুন:প্রতিষ্ঠার চেষ্টা থাকলেও তাতে যজ্ঞের উদ্দিষ্ট ঈশ্বর দেবতা নন। এভাবে উপনিষদে একক ব্ৰহ্মবাদ বা ঈশ্বরতত্ত্ব প্রাধান্য পেতে থাকে। তাই কঠোপরিষদ বলেন, পরব্রহ্মের ভয়েই দেবতারা তাঁহাদের নির্দিষ্ট কার্যক্রম পালন করে থাকে। বৃহদারণ্যকে এবং ছান্দোগ্যেও ১৯ তাই চরম কথা ঘোষিত হয়েছে–আত্মাই ব্রহ্ম।
মহাভারত
মহাভারতে বিষ্ণু ও বিষ্ণু অবতারের কথাই আছে। অন্য দেবতার অবতারের কথা নেই।২০ কাজেই বিষ্ণুই প্রাধান্য পেয়েছেন এ কাব্যে। অবশ্য বৈদিক দেব মণ্ডলে মহাভারতোক্ত দেব-দেবীরই, ঠাঁই হল। এতে দেবতারা একই ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত বিভিন্ন রূপ বা প্রকাশ এই মত গৃহী। হইল। সাংখ্য, যোগ, পাশুপত ও পঞ্চরাত্র যথাক্রমে কপিল, হিরণ্যগর্ভ শিব ও নারায়ণ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হইয়াছে। যোগ ও সাংখ্য মহাভারতে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। তাত্ত্বিক শিক্ষার দিক দিয়া এই মহাকাব্যে বিভিন্ন মতবাদ সকলের এক অসঙ্গতিপূর্ণ সংমিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়।….. মহাকাব্যে বর্ণিত তত্ত্ব-বিদ্যায় বিভিন্ন ভাবধারার পারস্পরিক প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়।….. এই সকলই প্রাথমিক সাংখ্যের স্বভাববাদী দ্বৈতমত ও প্রাথমিক যোগদর্শনের সাধারণ অঙ্গস্বরূপ ঈশ্বরবাদের দ্বারা প্রভাবিত। …. অপরদিকে আমরা পাশুপত, বৈষ্ণব, নারায়ণ ও প্রধান প্রধান ভাগবত সম্প্রদায় সকলের একেশ্বরবাদী ভক্তিবাদ দেখিতে পাই। এইগুলি বিভিন্ন উৎস হইতে তাহাদের ভাবধারা সকল সংগ্রহ করিয়াছিল।২২ মহাভারতের ধর্মীয় চিন্তাধারা ঈশ্বরনিষ্ঠ ও স্পষ্টত দ্বৈতবাদী।২৩ সাধারণ আর্যদের নিজস্ব বিশ্বাস ও আচার ব্যবহার অবশ্যই ছিল। কিন্তু এইগুলি উপত্যকার অনার্য সাংস্কৃতিক ভাবধারায় বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল (রুদ্র শিবের ধারণাতেই ইহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।) ….. ইহা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির যে-সংমিশ্রণ সম্ভবত বৈদিক যুগেই আরম্ভ হইয়াছিল তাহা বেদোত্তর যুগেও ধর্ম ও দর্শনের ক্রমবিকাশের সহায়তা করিয়াছিল। (এবং এইরূপে) বেদবিরোধী লোক প্রচলিত ধর্মসম্মত দেব-দেবী ও আচার নূতন ব্যাখ্যা দিয়া বৈদিক ধর্মের মধ্যেই সন্নিবিষ্ট করা হইল।…. (এইভাবে) রুদ্রশিব, বিষ্ণু-নারায়ণ অথবা কৃষ্ণ-বাসুদেবের উপাসনাকে কেন্দ্র করিয়া যে সকল লোকপ্রচলিত মত গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেইগুলির আবেগ-প্রধান ভক্তিবাদের দিকে বিশেষ প্রবণতা ছিল, ইহাতে প্রাচীন ক্রিয়াকাণ্ড ও ব্রহ্মমূলক ধর্মগত নিশ্চয়ই অনেকটা শিথিল হইয়া আসিতেছিল।
পুরাণ
Pargitar বলেন, সমষ্টিগতভাবে বিচার করিলে এইগুলি (পুরাণগুলি) প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় হিন্দুধর্মের ধর্ম-দর্শন, ইতিহাস, ব্যক্তি, সমাজ ও রাজনীতির একটি সর্বসাধারণের উপযোগী বিশ্বকোষ। পুরাণে অদ্বৈত, দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, ও বিশিষ্টাদ্বৈত এমনকি সাংখ্য, যোগ, ন্যায় প্রভৃতি বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদেরও সমন্বয় সাধন করিবার চেষ্টা আছে।২৬ পুরাণগুলোর মধ্যে বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত পুরাণই শ্রেষ্ঠ। সর্বপুরাণেরই সারকথা ও তাৎপর্য বিশেষ করে বিষ্ণুপুরাণে মেলে।২৭ ভাগবতের দর্শনে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, ইহাতে পুরাণসমূহের ঐশ্বরিক লীলাবাদের সহিত বেদান্ত দর্শনের মায়াবাদ, সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ, শৈব সম্প্রদায়ের শক্তিবাদ এবং মীমাংসা ও অন্যন্য সম্প্রদায়ের কর্মবাদের সমন্বয় সাধনের জন্য একটি সাতিশয় কলাকুশল প্রযত্ন করা হইয়াছে।
চার্বাক দর্শন
বৃহস্পতি লৌক্য বা ঋগ্বেদের ব্রাহ্মণস্পতি সর্বপ্রথম বস্তুকে চরম সত্য বলে ঘোষণা করেন। চার্বাকরা ছিলেন বৃহস্পতির মতানুসারী, এ কারণে তাদেরকে বাৰ্হস্পত্য বা লোকায়তিক বলা হয়। এরা বস্তুবাদী-অধ্যাত্মবাদী নন। বেদের আমল থেকে এঁদের ধারা অব্যাহত রয়েছে। তার আগেও যে লোকমনে এর জড় ছিল, তা অনুমান করা যায় বেদে এইমতের উল্লেখ থেকে। রামায়ণের আবালিমুনি, হরিবংশের রাজা বেন, গৌতম বুদ্ধের সমকালীন অজিত কেশকম্বলী, তাঁর শিষ্য পায়াসি, আর ভাগুরি, পুরন্দর প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে নাস্তিক্যবাদের ধারক ও বাহক ছিলেন। এ ধারার চিন্তার প্রসূন হচ্ছে ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, প্রাণাত্মবাদ ও মনশ্চৈতন্যবাদ। দেহের বিনাশে চৈতন্য লুপ্ত হয় এবং দেহের উপাদানগুলো নিজ নিজ ভূতে মিশে যায়; কাজেই কর্মফল ভোগ, আত্মার জন্মান্তর গ্রহণ ইত্যাদি অর্থহীন। জড় পদার্থ থেকে চৈতন্যের উৎপত্তি–এই মত বৃহদারণ্যক উপনিষদেও মেলে এবং দেহাত্মবাদের অনুকূলে ইঙ্গিত পাওয়া যায় ছান্দোগ্য উপনিষদের ইন্দ্রবিরোচন উপাখ্যানে।
জৈন–বৌদ্ধমত
সর্বজীবের প্রাণের মূল্যবোধ ও জীব নির্বিশেষের জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থেকেই অহিংসার জন্ম। এটি মানব-সংস্কৃতির ও সংবেদনশীলতার সর্বোচ্চ বিকাশের পরিচায়ক, মনুষ্যত্বের এমনি বিকাশ কালের দিক দিয়ে বিস্ময়কর। আদি তীর্থঙ্কর পার্শ্ব ঐতিহাসিক ব্যক্তি। মহাবীরের আড়াইশ বছর আগে তিনি জীবিত ছিলেন। গৌতম বুদ্ধের আগেও বহু বোধিসত্ত্ব আবির্ভূত হয়েছেন বলে বুদ্ধ দাবী করেছেন। কাজেই অহিংস মত আর্য আগমনের পূর্বেকার বলে মনে হয়। বর্ধমান মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব কাল এক আধ্যাত্মিক অস্থিরতার যুগ। (তখন) প্রাচীন ধর্মের বন্ধন হইতে সমাজ দ্রুত সরিয়া যাইতেছিল। হয়তো অনার্য যৌগিক ধ্যান, কৃঞ্জু সাধনা, জন্মান্তরবাদ, শিবপূজা প্রভৃতি অনার্য আচার-সংস্কার প্রবল হয়ে উঠেছিল। তাই বৌদ্ধমতে দেব, দ্বিজ ও বেদের প্রতি বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য চার্বাকরা আগে থেকেই এসবের প্রতি অবিশ্বাস ও বিরূপতা প্রচার করে চলেছিলেন। ব্রহ্মজাল সুত্ত মতে বৈদিক কর্মকাণ্ড বিরোধী সম্প্রদায় ছিল বহু এবং বিবিধ। এ সময়ে বিভিন্ন পন্থী তীর্থকগণ (নাস্তিক-আচার্য)–যথা, পুরাণ, কস্সপ, মকখলি, গোসাল, অজিত কেশকম্বলী, পকুধ-কচ্চায়ন, নিগন্থনাট পুত্ত, সঞ্জয়-বেলটুঠপুত্ত এবং আরো অনেক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণ্য মতবাদ বিরোধী প্রচারণা চালাতেন। বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীরাই পরবর্তীকালে সাধনপন্থ হিসেবে যোগাচার গ্রহণ করে।
সাংখ্য ও যোগ
বেদ ও কঠ, শ্বেতাশ্বতর ও মৈত্রায়নী উপনিষদে সাংখ্যসম্মত ধারণা লক্ষ্য করা যায়; কাজেই সাংখ্য মত নিশ্চয়ই প্রাচীনতর। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকের পূর্ববর্তী নয়। তবু সাংখ্য মত যে ভারতের প্রাচীনতম লোকায়ত দর্শন, তা নানা কারণে অস্বীকার করার উপায় নেই। আড়ার কলমের নিকট গৌতম বুদ্ধের সাংখ্য দর্শন শিক্ষা, ন্যায়সূত্রে এবং ব্রহ্মসূত্রে সাংখ্য দর্শনের মৌলিক মতগুলির সমালোচনা প্রভৃতি থেকেও এর প্রাচীনতা অনুমান করা সম্ভব। গীতায় সাংখ্য ও যোগকে অভিন্ন বলা হয়েছে। …. যোগ হচ্ছে সাংখ্যের ব্যবহারিক প্রয়োগ। যোগ ও সাংখ্যের দার্শনিক ভিত্তি একই। পতঞ্জলি তার যোগসূত্রে ঈশ্বর-রূপ যে অপর একটি তত্ত্বের অবতারণা করেছেন তার জন্যই এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য।৩৫
আমরা ভারতিক অভিজাতশ্রেণীর ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন ধারার কিছুটা পরিচয় পেলাম। এতে আমরা দেখেছি দেশীয় গণমানসপ্রসূত নানা মত উঁচুস্তরের মানুষের ধর্মে ও দর্শনে বার বার হানা দিয়ে নিজেদের ঠাই করে নিয়েছে। এবার সে গণমানস উদ্ভূত ধর্মসংস্কার ও দেবতার পরিচয় নেওয়া যাক।
ভয় থেকেই বিশ্বাসের উৎপত্তি। ভয় কিসের? ভয় অপ্রাপ্তির, ক্ষতির এবং অ-সুখের। আত্মরক্ষা, আত্মপ্রসার ও আত্মস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে যা আবশ্যক তা পাওয়ার আকাক্ষার নাম বাঞ্ছা। বাঞ্ছামাত্রই চেষ্টা সত্ত্বেও সিদ্ধ হয় না। নিজের অসামর্থ্য আছে, আছে আরো অজানা অকারণ বাধা। এই বাধাস্বরূপ অজ্ঞাত শক্তিই অমূর্ত অরি-শক্তি, আর সিদ্ধির সহায়ক শক্তি হচ্ছে ইষ্ট-শক্তি। এই অরি-শক্তির দমন ও ইষ্ট-শক্তির আবাহন প্রয়াসই জাদু-বিশ্বাসে প্রবর্তনা দিয়েছে। বাঞ্ছ-সিদ্ধির আত্যন্তিক কামনা থেকেই জাদু-বিশ্বাস উৎসারিত। আদি অমূর্ত জাদু বিশ্বাস পরে পরে প্রমূর্ত ইষ্ট ও অরি দেবতার রূপ নিয়েছে।
এদেশের এক দেবতা গণপতি গণেশ। ইনি ছিলেন আদিতে অরি দেবতা-বিঘ্নরাজ। ইনি অনার্য দেবতা।৩৭ ভিলেরা চাষাবাদের প্রারম্ভে শিলাখণ্ডে সিন্দুর মেখে গণেশরূপে পূজা করে। ঋগ্বেদেও গণপতির উল্লেখ রয়েছে। ঋগ্বেদে গণপতি ও বৃহস্পতি অভিন্ন। লোকায়ত মতের প্রবর্তক বলে পরিচিত বৃহস্পতি ও বৈদিক বৃহস্পতি অবশ্য অভিন্ন কী না, বলা যাবে না। ভারতের বিভিন্ন স্থানে নগ্ননারীর সঙ্গে মৈথুনরত গণেশ মূর্তি পাওয়া গেছে। আনন্দগিরির শঙ্কর বিজয় এর সতেরো সংখ্যক প্রকরণে আছে যে গাণপত্য মতে গণেশ বামাচারের সঙ্গে সংযুক্ত। এতেই বোঝা যায়, আদি মৈথুনতত্ত্ব থেকেই গণপতি গণেশ দেবতার পৌরাণিক রূপান্তর ঘটেছে।
.
০৪.
॥ তন্ত্র ॥
ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অনার্যের ধর্ম বা সংস্কার হিসেবে তন্ত্রের ব্যাপকতা দেখেই এক বিদ্বান বলেছেন:
In the popular knowledge and belief they have practically superseded the Vedas over a large part of India. In all writings (Tantric writings) these female principle is personified and made prominent to the almost total exclusion of the male.
তান্ত্রিক সাধনায় নারীর গুরুত্ব যে অত্যধিক তার সাক্ষ্য আচারভেদ তন্ত্রেও আছে :
পঞ্চতত্ত্বং খপুষ্পঞ্চ পূজয়েৎ কুলঘোষিতম্।
বামাচারো ভবত্ত এবামাভূত্বা যজেৎ পরাম ॥
শাক্তদের সাধনাও এরূপ। R. G. Bhandarkar বলেন :
The ambition of every pious follower of the system (sakta) is to become identical with Tripura-Sundari, and one of his religious exercises is to habituate himself to think that he is a woman.
সহজিয়াদের সাধনতত্ত্বও এরূপ। মনীন্দ্রমোহন বসু বলেন :
The sahajias also believe that at a certain stage of spiritual culture the man should transform himself into a woman and remember that he cannot have the experience of true love so long as he cannot realise the nature of woman in him.
এখানে বৈষ্ণবের রাধাভাব ও গোপীভাব স্মর্তব্য।
তন্ত্রমতে পুরুষ ও প্রকৃতির আদি মৈথুন থেকেই বিশ্বের উৎপত্তি।৪ সাংখ্যেও তাই। বাচ্যবস্তুটিকে স্ত্রীরূপেই সাংখ্য কল্পনা করিয়াছে। প্রকৃতি পুরুষকে মোহিত করে, যেমন নারী পুরুষকে বশ করে, প্রকৃতির ক্রিয়া ও নারীর লাস্য ও হাস্য এবং ভাবও ভাবের অনুরূপ কল্পিত হইয়াছে। চীনেও বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে এই ধারণাই ছিল। সৃষ্টি হচ্ছে Yang (পুরুষ) ও Yin (নারী) 49 cita avangal 2007 1 He (man) is described as a Microcasm-a world in miniature এ সব দেখে নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করতে হয় যে ভারতের অনার্য সমাজে মিথুনতত্ত্ব, জাদু বিশ্বাস এবং মাতৃ বা ক্ষেত্র প্রাধান্য ছিল। ময়েনজোদাড়োর আবিক্রিয়া এবং দ্রাবিড় সমাজের নারীদেবতা প্রভৃতি এ বিশ্বাসের অনুকূল। দেবীপ্রসাদ বলেন, আমাদের যুক্তি অনুসারে, তন্ত্রের মতোই ওই সহজিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলিও আদিম কৃষিকেন্দ্রিক জাদুবিশ্বাস থেকেই জন্মলাভ করেছে। পাঁচকড়ি বানার্জি বলেন–তন্ত্রের যে-কোনো পুথি পাঠ কর না কেন, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যাইবে যে, অতি পুরাতন একটা শক্তি ধর্মের বুনিয়াদের উপর বৌদ্ধ মনীষা একটা নতুন ধর্মের প্রসাদ গড়িয়া তুলিয়াছেন। পরে নব্যহিন্দুর ব্রাহ্মণ-প্রতিভা বৌদ্ধের সেই মনীষা-প্রাসাদের উপর ব্রাহ্মণ্যের লেখা গাঢ় করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন। তন্ত্রতত্ত্ব সম্বন্ধে পাঁচকড়ি বানার্জি বলেন, যাহা আছে ভাণ্ডে, তাহাই আছে ব্রহ্মাণ্ডে–ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণা : সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে। ইহাই সকল তন্ত্রের সিদ্ধান্ত। ….. তন্ত্র বলিতেছেন যে যখন ব্রহ্মাণ্ড ও দেহভাণ্ড একই পদ্ধতি অনুসারে, একই রকমের উপাদান সাহায্যে নির্মিত, উভয়ের মধ্যে একই পদ্ধতির খেলা হইতেছে, তখন দেহগত শক্তির উন্মেষ ঘটাইতে পারিলে ব্রহ্মাণ্ডের শক্তি তোমার অনুকূল হইবে। …. এদেশের সিদ্ধগণ বলেন যে মনুষ্যদেহের মতো পুর্ণাবয়ব যন্ত্র আর নাই। …. অতএব এই যন্ত্রস্থ সকল গুপ্ত এবং সুপ্ত শক্তির উন্মেষ ঘটাইতে পারিলে অন্য কোনো স্বতন্ত্র যন্ত্র ব্যতিরেকে তোমার বাসনা পূর্ণ হইতে পারে। এই উক্তির সমর্থন পাই ছান্দোগ্যে, বিরোচন বলেছেন, এই পৃথিবীতে দেহেরই পূজা করিবে, দেহেরই পরিচর্যা করিবে। দেহকে মহীয়ান করিলে এবং দেহের পরিচর্যা করিলেই ইহলোক ও পরলোক–এই উভয়লোকই লাভ করা যায়।
শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে, বাঙলাদেশে এবং তৎসলগ্ন পূর্ব-ভারতীয় অঞ্চলসমূহে এই তন্ত্রপ্রভাব খ্রীস্টীয় অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত মহাযান বৌদ্ধধর্মের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়া মহাযান বৌদ্ধধর্মকে বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি তান্ত্রিক ধর্মে রূপান্তরিত করিয়া দিয়াছিল। ….. বাঙলাদেশে যত হিন্দুতন্ত্র প্রচলিত আছে, তাহা মোটামুটিভাবে খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতক হইতে খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যে রচিত। …. ভারতবর্ষের তন্ত্রসাধন মূলত: একটি সাধনা।…. এই তন্ত্রসাধনার একটি বিশেষ ধারা বৌদ্ধ দোহা কোষ এবং চর্যাগীতিগুলির ভিতর দিয়া যে সহজিয়ারূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারই ঐতিহাসিক ক্রমপরিণতি বাংলাদেশের বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনায় এবং বিশেষ বিশেষ বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে। এবং সপ্তদশ শতক হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা এখানে একটা নবরূপ লাভ করিয়াছে এবং এই নবরূপেই বাঙলার সমাজ-সংস্কৃতিকে তাহা গভীর প্রভাবান্বিত করিয়াছে। এজন্যেই পাঁচকড়ি বানার্জি বলেছেন, সহজিয়া, বৈষ্ণব, শৈব, কিশোরী ভজা, কর্তাভজা, পরকীয়া-সাধনা সবই রিরংসার উপর প্রতিষ্ঠাপিত।
এই দেহতেই কৈলাস, এই দেহতেই হিমালয়, এই দেহতেই বৃন্দাবন, এই দেহতেই গোবর্ধন, এই দেহাভ্যন্তরেই হরগৌরী বা কৃষ্ণরাধিকা নানা লীলানাট্য প্রকাশ করিতেছেন। তাই তান্ত্রিক, যোগী, সহজিয়া বাউল সবাই দেহচর্যাকেই মূত্রত করেছে। আবার তান্ত্রিক ও সহজিয়ারা রতিপ্রয়োগে এবং নাথযোগীরা রতিনিরোধে এ সাধনা করে। যৌগিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এ সাধনা চলে, যোগ তাই বামাচারী ও বামাবর্জিত–এই দুই প্রকার। কামনিরোধ যোগাচার সম্বন্ধে শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন:
The most important of the secret practices, is the yogic control of the sex-pleasure so as to transform it into transcendental bliss, which is at the same time conducive to health both of the body and the mind.
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন, যোগাচারমতে যেমন কিছুই থাকে না, বিজ্ঞানমাত্র থাকে; সহজমতে তেমনি কিছুই থাকে না, আনন্দ মাত্র থাকে। এই আনন্দকে তাঁহারা সুখ বলেন, কখনো বা মহাসুখ বলেন, সে-সুখ স্ত্রীপুরুষ সংযোগজনিত সুখ। তন্ত্রের মতো এখানে নারীশক্তিই মুখ্য। তাই শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেন :
Another thing that deserves special attention in connection with the yogic practce of the sahajia Buddhists is the conception of the female force. In the charya songs we find frequent reference to this female force variously called as the chandi, Dombi, Savari, Yogini, Nairamani, Sahaja-Sundari etc. and we find frequent mention of the union of the yogin with this personified female deity … This conception of Sakti of the Buddhist-Sahajias is an adoption of the general Tantric conception of the sakti.
আদি মৈথুনতত্ত্ব থেকে এসব বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভবের ধারাবাহিক ইতিহাস দেওয়া সম্ভব নয়। তবু পরোক্ষ ও বিচ্ছিন্ন প্রমাণে এটুকু বোঝা যায়, আদি কৃষিজীবীরা মৈথুনতত্ত্বের বিকাশ লোকায়তে এবং তার পরিণতি শিব-শিবানী, মায়া-ব্রহ্ম, রাধা-কৃষ্ণ, প্রজ্ঞা-উপায় প্রভৃতি রস-রতি তত্ত্বে বা বিজ্ঞানবাদে।
মহাভারতের উদ্দালক ও তৎপুত্র শ্বেতকেতুর উপাখ্যান (আদিপর্ব, ১২২ অধ্যায়) থেকে জানা যায় তখনও গাভীগণের মতো স্ত্রীগণ শতসহস্র পুরুষে আসক্ত হলেও তারা অধর্মলিপ্ত হয় না। বরং এরূপ আসক্ত হওয়াই নিত্যধর্ম। কাজেই তখনও নারীর একনিষ্ঠতাজাত সতীত্ব ধারণা গড়ে উঠেনি।
বাৰ্হস্পত্য সূত্ৰমে আছে : সর্বথা লোকয়তিকমেব শাস্ত্রমর্থসাধনকালে কাঁপালিকমের কামসাধনে।
গুণরত্ন বলেছেন–কাঁপালিক ও লোকায়তিকের মধ্যে কোনো তফাৎ নেই। লোকায়তিকেরা গায়ে ভস্ম মাখে, মদ খায়, মাংস খায় এবং তারা মৈথুনাসক্ত ও যোগী। এবং বছরের এক নির্দিষ্ট দিনে তারা সবাই একস্থানে মিলিত হয়ে মৈথুনে রত হয়। মাধ্বাচার্য বলেছেন, লোকায়তিকেরা কামাচারী–অর্থ ও কামসাধনাই তাদের লক্ষ্য।
গুণরত্নকথিত মৈথুন-উৎসব আজো হয়। সাঁওতাল, হো, পাঞ্চা, কোটার প্রভৃতি দেশী সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং চিলি, নিউমেক্সিকো, নিকারাগুয়া, মেক্সিকো প্রভৃতি বিদেশী আদিবাসীর মধ্যে তা চালু আছে। গুণরত্ন বলেছেন, চার্বাকরা (লোকায়তিকরা)
They drank wine and ate meat and were given to unrestricted sex indulgence. Each year they gathered together on a particular day and had unrestricted intercourse with women. They behaved like common people and for this reason they were called Lokayata.
সাঁওতালেরা এমনি উৎসব আজো করে।
Five days are spent in dancing, drinking and debauching. It is significant that at the commencement the village headman gives a talk to the village-people in which he says that they may act as they like sexually, only being careful not to touch certain women, otherwise they may amuse themselves. The village people reply that they are putting twelve balls of cotton in their ears and will not pay any heed to, nor hear or see anything.
এরই বিকশিত তাত্ত্বিকরূপ পাই পরবর্তী ধর্মমতগুলোতে। হরপ্রসাদ সে-মতগুলোর কথা এভাবে বলেছেন :
The influence of the Lokayatas and Kapalikas is still strong in India. There is a sect and numerous ones too, the followers of which believe that Deha, or the material human body is all that should be cared for and their religious practices are concerned with the Union of men and women and their success (siddhi) varies according to the duration of the union. They call themselves Vaisnavas, but they do not believe in Vishnu or Krishna or their incarnations. They believe in Deha. They have another name Sahajia, which is the name of a sect of Buddhists which arose from Mahayana in the last four Centuries of their existence in India.
দোল, হোলী বা মদনোৎসবে আজো সেই মৈথুন উৎসবের রেশ রয়ে গেছে। W. Crooke এই হোলী বা মদনোৎসবের মূলে মানুষ, পশু ও শস্যের উর্বরতা বাড়ানোর কামনা ছিল বলে অনুমান করেছেন।
অতএব, আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে এই : সৃষ্টিসম্ভব মৈথুনতত্ত্ব থেকে সাংখ্যতত্ত্বের উদ্ভব। এই তত্ত্বের প্রকৃতির উপর আত্যন্তিক গুরুত্বদানের ফলে তন্ত্রমত এবং পুরুষের উপর গুরুত্বদানের কারণে লিঙ্গায়েত মত ও যোগ-পদ্ধতির বিকাশ। নিজের মধ্যে অলৌকিক শক্তির উদ্বোধন ও প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে এ সাধনার লক্ষ্য। তাই মূলত এটি শক্তিবাদ। যোগপদ্ধতি, তান্ত্রিক আচার অথবা যোগতান্ত্রিক মিশ্র আচার মাধ্যমে এই শক্তিকে আয়ত্তে আনার প্রয়াস চলেছে। যেখানে শক্তিস্বরূপা প্রকৃতি প্রাধান্য লাভ করেছেন, সেখানে শাক্তধর্ম বা শাক্তশাস্ত্রের উদ্ভব, যেখানে শক্তিমান শিব বা বিষ্ণু গুরুত্ব পেয়েছেন, সেখানে শৈব বা বৈষ্ণব মতবাদের উদ্ভব। যোগ ও তন্ত্র প্রায় সব মতবাদকে প্রভাবিত করেছে। যারা অধ্যাত্ম সাধনাকে জীবনের একমাত্র ব্রত করে নেয়, সে-সব সাধকের সাধনার আবশ্যিক অঙ্গ হয়েছে তন্ত্র অথবা যোগ। বাঙলা দেশে পাল আমলে আদি অনার্য-সংস্কার ব্রাহ্মণ্যমত এবং মহাযান বৌদ্ধ মতের সমন্বয়ে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, মন্ত্রযান-বজ্রযান-কালচক্রযান ও শেষে সহজযান সম্প্রদায়ের উদ্ভব। মন্ত্র, যন্ত্র, বীজ, মুদ্রা, মণ্ডল, লতা, ভগ, যোগ ও নানা গুহ্যপ্রক্রিয়াই এসব মতের ভিত্তি। এবং সাধারণভাবে আসন, ন্যাস, দেবতার প্রতীক বর্ণরেখাত্মক যন্ত্র, যোগ-ক্রিয়া, দীক্ষাগ্রহণ এমনকি সম্প্রদায় বিশেষে মূর্তিপূজার মাধ্যমেই উপাসনা চলে। বাঙলা। দেশে অষ্টাদশ শৈব আগম নিঃসন্দেহে গুপ্তযুগে রচিত হয় এবং খুব সম্ভব গুপ্তযুগের শেষের দিকে ও পালযুগে তান্ত্রিক শক্তিপূজার প্রচলন হয়। বর্তমান হিন্দু পূজাপদ্ধতিতেও তান্ত্রিক পদ্ধতির প্রভাব . লক্ষণীয়। মনে হয় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মধ্যে গীতার কর্মবাদ ও শঙ্করের জ্ঞানবাদ এবং উচ্চশ্রেণীর অনার্যদের মধ্যে ভক্তিবাদ ও নিম্নশ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে যোগ ও তন্ত্র প্রাধান্য লাভ করেছিল। এর থেকেই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম, মন্ত্রযান-বজ্রযান-কালচক্রযান-সহজযান ও নাথপন্থের উদ্ভব। এর জের রয়েছে বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউল মতে। এই তত্ত্বসাধনার একটি ধারা বৌদ্ধ দোহাকোষ ও চর্যাগীতির ভিতর দিয়া যে সহজরূপ লাভ করিয়াছে, তাহারই ঐতিহাসিক ক্রমপরিণতি বাঙালাদেশের বৈষ্ণব সহজিয়াসাধনায় এবং বিশেষ বিশেষ বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে।২২ এবং সহজিয়া ধর্মের সহিত সাদৃশ্য থাকায় সুফীবাদের সামঞ্জস্য বিধান হইয়া বাউল সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মণ্য শৈব ও বৌদ্ধ সহজিয়ার সমবায়ে গড়ে উঠেছে একটি মিশ্ৰমত–যার নাম। নাথপন্থ। বামাচার নয়, কায়াসাধন তথা দেহতাত্ত্বিক সাধনাই এদের লক্ষ্য। হঠযোগের মাধ্যমেই এ সাধনা চলে। একসময় এই নাথপন্থ ও সহজিয়ামতের প্রাদুর্ভাব ছিল বাঙলায়। চর্যাগীতি ও নাথ সাহিত্য তার প্রমাণ। এ দুটো সম্প্রদায়ের লোক পরে ইসলামে ও বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়। কিন্তু পুরোনো বিশ্বাস-সংস্কার বর্জন করা সম্ভব হয়নি বলে ইসলাম ও বৈষ্ণব ধর্মের আওতায় থেকেও এরা নিজেদের পুরোনো প্রথায় ধর্মসাধনা করে চলে, তার ফলেই হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বাউল মতের উদ্ভব। সুফী মতের ইসলাম সহজেই বাঙ্গালার প্রচলিত যোগমার্গ ও অন্যান্য সাধনমার্গের সঙ্গে একটা আপোষ করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল।ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে মুসলমান মাধববিবি ও আউল চাঁদই বাউলমতের প্রবর্তক এবং মাধববিবির শিষ্য নিত্যানন্দ-পুত্র বীরভদ্রই (বা বীরচন্দ্র) বাউলমত জনপ্রিয় করেন। এ মতের সমর্থন মিলেছে বীরভদ্রের শিক্ষামূলক কড়চা নামের এক অজ্ঞাতপ্রায় পুথিতে। নিত্যানন্দ তাঁর পুত্র বীরদ্রকে বলছেন :
শীঘ্র করি যাহ তুমি মদিনা শহরে …
তথা যাই শিক্ষা লহ মাধববিবির সনে
তাহার শরীরে প্রভু আছেন বর্তমানে।
মাধববিবি বিনে তোর শিক্ষা দিতে নাই
তাঁহার শরীরে আছেন চৈতন্য গোঁসাই।
ডক্টর সুকুমার সেনের মতে, মহাযানের উপাস্য নরদেবতা অবলোকিতেশ্বর বাংলাদেশে লোকনাথ নাম নিয়ে বিষ্ণুর রূপান্তরে পরিণত হয়েছিলেন। …. বৌদ্ধযুগে বাংলাদেশে লোকনাথকে আশ্রয় করে ভক্তিধর্মের অঙ্কুর উদাত হয়েছিল। ….. বাংলাদেশে শাস্ত্রীয় বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে যেমন পূর্বেকার ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ভক্তিবাদের যুক্তবেণী প্রবাহিত হয়ে এসেছে, তান্ত্রিক বৈষ্ণব অর্থাৎ বাউল সহজিয়া ইত্যাদি মতের মধ্যে তেমনি পূর্বযুগের শৈব ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতবাদের পরিণতি দেখা যায়। অষ্টম শতাব্দী কিংবা তারও পর থেকে বাংলাদেশে অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে তান্ত্রিকভাবের দুটি ধর্মমত চলিত ছিল–শৈবনাথমত এবং বৌদ্ধ সহজিয়ামত। এই দুই মতের সাধনায় ও দর্শনে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। নাথ সন্ন্যাসীরা নিজেদের যোগী বা কাঁপালিক বলত, এরা কানে নরাস্থি কুণ্ডল, কণ্ঠে নরাস্থি মালা, পায়ে নূপুর ও হাতে নরকপাল ধারণ করত এবং গায়ে ছাই মাখত। এদের আহার বিহার ছিল কদর্য, তাই গ্রামের বাহিরে ছিল এদের কুঁড়েঘর। যোগীদের নামের শেষে শব্দ হত নাথ। বর্তমান সময়ে যুগী জাতির (তাঁতি) মধ্যে নাথ পদবী ও পূর্বেকার আচার অনুষ্ঠান কিছু কিছু চলিত আছে। বৌদ্ধ সহজ সাধকেরা দেহতত্ত্বের সাধনা করত এবং আবশ্যক হলে যোগিনী বা অবধূতী অর্থাৎ সাধক-সঙ্গিনী গ্রহণ করত। এদের সাধনার সঙ্গে নিহিত আছে চর্যাপদে। ছকে ফেলে দেখলে বাঙলার তান্ত্রিক ধর্মের বিবর্তন এরূপ দাঁড়ায় :
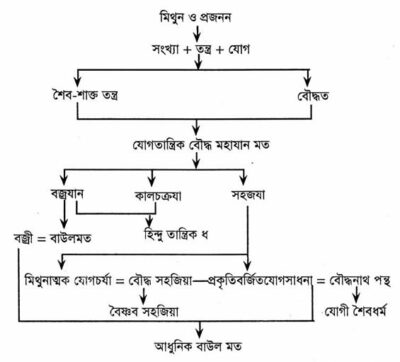
তন্ত্রিক শৈব–শাক্ত ধর্ম
তন্ত্র হচ্ছে ভোগ-মোক্ষবাদ–ভোগের মাধ্যমে মোক্ষলাভই আদর্শ। নারীই জগত্তারণ আদ্যাশক্তি। তিনিই মহামায়া, কালী, তারা, শিবানী। নারীশক্তিতেই পুরুষ হয় শক্তিমান। শিব হচ্ছেন শক্তিমান। শিবশক্তি অদ্বয়ও বটে, ভিন্নও বটে। শক্তি সাধনায় শক্তিমান হওয়া তথা শিবত্ব উপলব্ধি করাই তান্ত্রিক সাধনার লক্ষ্য। এর সঙ্গে বৌদ্ধ বোধিচিত্ত বা মহাসুখ তুলনীয়। এ সাধনায় প্রকৃতিসঙ্গ প্রয়োজন। মৈথুনে বীর্যধারণের দরকার হয় না। রেতক্রিয়া অবিধেয় নয়। এ সাধনা করতে হয় নারীভাবে–বামা ভুত্বা যজেৎ পরাম। লতা, ভগবান-যন্ত্র, পদ্ম তথা নারীর যোনি-প্রতিম পূজার উপাদান। আসন, ন্যাস, মুদ্রা, মূলমন্ত্র, বীজমন্ত্র, বর্ণরেখাত্মক যন্ত্র, যোগক্রিয়া, দীক্ষা গ্রহণ প্রভৃতি সাধনার অঙ্গ। এরা গুরুবাদী। সাধনাও গুহ্য। পঞ্চ মকারে তথা মাংস, মৎস্য, মদ্য, মুদ্রা ও মৈথুনে এরা বিশেষ আসক্ত। এরাও পরকীয়া বামা মৈথুনই প্রকৃষ্ট পন্থা বলে মানে। এদের গুরু চার প্রকার–গুরু, পরমগুরু, পরমেষ্টি গুরু ও পরাৎপর গুরু। তারা সবাই শিবের অংশ। হিন্দুতন্ত্রে মেরুদণ্ডকে আশ্রয় করে পর পর ছয়টি চক্র (ষটচক্র-মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা চক্র (দ্বিদল চক্র) ও তাদের সন্নিহিত পদ্ম, এবং ইড়া (গঙ্গা) পিঙ্গলা (যমুনা) সুষুম্না (সরস্বতী) প্রভৃতি বহু নাড়ির কল্পনা করা হয়েছে। সর্বনিম্নের চক্রের নাম মূলাধারচক্র। এতেই সৃষ্টিরূপা কুণ্ডলিনী সুষুপ্ত রয়েছে। ষট্চক্রের ঊর্ধ্বে রয়েছে সহস্রার (সহস্রদলপদ্ম), তাতে থাকেন পরম শিব। যৌগিক প্রক্রিয়ার দ্বারা এই কুণ্ডলিনীকে ক্রমাগত ঊর্ধ্বে নিয়ে পরম শিবের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে ত্রিগুণাতীত শিবত্ব উপলব্ধি হয়। এটি এক পরমানন্দময় অদ্বয়সত্তা–শিবশক্তির অদ্বয়সত্তা–এই মিলনজাত কেবলানন্দই সাধকের চরম আধ্যাত্মিক লক্ষ্য। শিব পুরুষশক্তির প্রতীক–উমা নারীশক্তির প্রতীক–উভয়ের মিলনজনিত যে সামরস্য তাই কেবলানন্দ, বৌদ্ধ তান্ত্রিকের মহাসুখ ও বৈষ্ণব সহজিয়ার মহাভাবরূপ সহজাবস্থা। মূল পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বই হিন্দুর শিবশক্তি, বৌদ্ধের প্রজ্ঞা-উপায় এবং বৈষ্ণব ও বৈষ্ণব সহজিয়ার রাধাকৃষ্ণতত্ত্বে রূপ নিয়েছে।
শাক্তমন্ত্রে বামাচার ও দক্ষিণাগার নামে দুই সাধনপদ্ধতি আছে। বামাচার পঞ্চ ম-কার ভিত্তিক। আর দক্ষিণাগার ম-কার বর্জিত যোগনির্ভর।
ছকে হিন্দুতন্ত্র
চক্র ——- দেহস্থান ——- পদ্মদল অধিষ্ঠাত্র দেবতা
১. মূলাধার—– গুহ্যদেশ ও জননেন্দ্রিয়ের মধ্যস্থ ৪ —- ব্রহ্ম + ডাকিনী
২. স্বাধিষ্ঠান ——– জননেন্দ্রিয়ের মূলে সুষুমম্নর মধ্যস্থ চিত্রিনী নাড়ীস্থ ৬ — মহাবিষ্ণু + রাকিনী
৩. মণিপুর ——– নাভিমূলে ১০ ——– রুদ্র + লাকিনী
৪. অনাহত —— বক্ষ ১২ ——— ঈশ + কাকিনী
৫. বিশুদ্ধ ——- কণ্ঠ ১৬ ———— অর্ধনারীশ্বর (শিবশক্তি) + শাকিনী
৬. আজ্ঞা ——- ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যস্থ ২ —- পরশিব + হাকিনী
এর উপরে রয়েছে সহস্রদলপদ্ম, নাম সহস্রার। এটি পরমশিব ও কুণ্ডলিনীর মিলনস্থল। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না প্রভৃতি নাড়িই বায়ুপ্রবাহ পথ। ইচ্ছামতো বায়ু সঞ্চালনই যোগক্রিয়ার মূলভিত্তি। তাই নাড়ির সঙ্গে যোগের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। অবশ্য খুঁটিনাটি ব্যাপারে বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থে কিছু কিছু অনৈক্যও রয়েছে। বিভিন্ন পদ্ধতির তান্ত্রিক সাধনার মধ্যে দিব্যাচার, সমায়াচার, দক্ষিণাচার ও পশ্বাচার প্রভৃতি নামমাত্র তান্ত্রিক আচার। যথার্থ তান্ত্রিক আচার হচ্ছে : বীরাচার, বামাচার, চীনাচার ও কুলাচার। কৃষ্ণানন্দের তন্ত্রসারই স্বীকৃত, নির্ভরযোগ্য ও জনপ্রিয় গ্রন্থ। বেশ্যা, নটী, রজকী, ব্রাহ্মণী প্রকৃতিই যোগ্য সাধন সঙ্গিনী।
বৌদ্ধতন্ত্র
প্রকৃতি ও পুরুষকে বৌদ্ধতন্ত্রে প্রজ্ঞা ও উপায় নামে অভিহিত করা হয়। হিন্দুতন্ত্রের ঘটচক্র বা পদ্ম বৌদ্ধতন্ত্রে চারচক্র বা পদ্ম। এবং তা কায়রূপে পরিকল্পিত। প্রথম চক্রটি নাভির নিচে অবস্থিত। এর নাম নির্মাণকায়। দ্বিতীয় চক্ৰ হৃদয়দেশে অবস্থিত। এর নাম ধর্মকায়। তৃতীয় চক্র কণ্ঠদেশে। এর নাম সম্ভোগকায়। চতুর্থটি ব্রহ্মতালুতে অবস্থিত। এর নাম সহজকায়। এই সহজকায় বা উষ্ণীষ কমলকে মহাসুখচক্র বা মহামুখকমলও বলা হয়। হে বতন্ত্র অনুসারে জননেন্দ্রিয়ের স্থান হইতে চেতন-অচেতন সমস্ত প্রাণীর উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া ঐ প্রদেশে নির্মাণকায় স্থাপিত হইয়াছে। ধর্মচক্র সমস্ত ধর্মের তত্ত্বরূপ বলিয়া হৃৎপ্রদেশে স্থাপিত, সম্ভোগ অর্থে ষড়রস সম্ভোগ, সম্ভোগকায় আনন্দ-রস সম্ভোগস্বরূপ, ইহা কণ্ঠদেশে স্থাপিত। মহাসুখচক্র তথা মহাসুখকায় মস্তকে স্থাপিত।
দেহস্থান — চক্র বা — কায় —- পদ্ম — মুদ্রা –– আনন্দ — দেবী — ক্ষণ
নাভি–নির্মাণচক্র–কায়–-নাভিপদ্ম চৌষট্টিদল–-কর্মমুদ্রা–-আনন্দকায়—লোচনা—বিচিত্র
হৃদয়—ধর্মচক্র–কায়–হৃৎপদ্ম বত্রিশ দল–ধর্মমুদ্রা–পরমানন্দ–মানকী–বিপাক
কণ্ঠ–সম্ভোগচক্র–কায়–কণ্ঠ পদ্ম ষোড়শ দল—মহামুদ্রা–বিরমানন্দ—পাত্র–বিমর্দ
মস্তক—সহজচক্র–উষ্ণীষ পদ্ম চতুর্দল—সময়মুদ্রা—সহজানন্দ—তারা– বিলক্ষণ
এদের সঙ্গে রয়েছে চার সাধনাঙ্গ–সেবা, উপসেবা, সাধনা ও মহাসাধনা।
চার আর্য সত্য– দুঃখ, দুঃখের কারণ, দুঃখ নিবৃত্তি, নিবৃত্তির উপায়।
চার তত্ত্ব —আত্মতত্ত্ব, মন্ত্ৰতত্ত্ব, দেবতাতত্ত্ব ও জ্ঞানতত্ত্ব।
এর সঙ্গে চার নিকায়, ঘোড়শ সংক্রান্তি, চৌষট্টি দণ্ড ও চার প্রহরাদির সম্পর্ক রয়েছে। আবার কোনো কোনো গ্রন্থে (যেমন সেকোদ্দেশ টীকা) কায়-বাক-চিত্ত-জ্ঞান অনুসারে প্রত্যেকের চার প্রকার ভেদ ধরে মোট ষোলো প্রকার আনন্দ নির্দেশ করা হয়েছে। বৌদ্ধতন্ত্রে ইড়া নাড়ির নাম ললনা, আলি, ধমন, চন্দ্র প্রভৃতি। পিঙ্গলার নাম রসনা, কালি, চমন, সূর্য প্রভৃতি। সুষুম্না নাড়ি, অবধূতী, দেবী, প্রজ্ঞা, নৈরাত্মা, যোগিনী, সহজ সুন্দরী প্রভৃতি নামে পরিচিত। বৌদ্ধতন্ত্রে ললনাকে প্রজ্ঞা (চন্দ্র) এবং রসনাকে উপায় (সূর্য) বলা হয়েছে। এ দুটো নাড়ির মিলন হয় অবধূতীতে। এ মিলন প্রজ্ঞা-উপায়ের মিলন। ললনা বিন্দু বহন করে, রসনা রজ: বহন করে, অবধূতী বহন করে প্রজ্ঞা-উপায় মিলনজনিত বোধিচিত্তকে। এই অবধূতীই সহজানন্দ স্বরূপিণী।
বৌদ্ধতন্ত্র সাধনায় হঠযোগের গুরুত্ব অত্যধিক। কেননা বিন্দুধারণ এবং তা ঊর্ধ্বে সঞ্চালনই এর লক্ষ্য। খড়গ, অঞ্জনা, পাদলেপা, অন্তর্ধান, রস রসায়ন, খেচর, ভূচর ও পাতাল বৌদ্ধতন্ত্রের এই অষ্টসিদ্ধি (সাধনমালা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫০)। নটী, রজকী, ডোমনী, চণ্ডালী ও ব্রাহ্মণীই সাধন সঙ্গিনীরূপে বিশেষ উপযোগী। যোগিনী-ডাকিনীরা সিদ্ধিপ্রভাবে অলৌকিক শক্তিধর হয়।
মহাযান বৌদ্ধমত উদ্ভূত উপমত সমূহ
বৌদ্ধধর্মে মন্ত্রের প্রচলন কবে থেকে হয়, তা সঠিক বলা যায় না। ডক্টর বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মতে বুদ্ধের সময় থেকেই বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা প্রবেশ করে, বুদ্ধদেবই সাধারণ অশিক্ষিত লোকদের জন্য মুদ্রা, মন্ত্র প্রভৃতি প্রবর্তন করেন। মন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাসই তান্ত্রিকতার ভিত্তি। বৌদ্ধগ্রন্থে মন্ত্রকে বলত ধারণী (যাহা দ্বারা কিছু ধারণ করা যায়)। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বলেন, খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকেই বৌদ্ধতন্ত্রগুলো রচিত হতে থাকে। এ সময় বৌদ্ধ ক্ষান্তি-পারমিতা দান-পারমিতা প্রভৃতি তত্ত্ব দেবীরূপে কল্পিত হয়ে প্রমূর্তরূপে পূজা পেতে থাকেন। ধারণী বা বীজমন্ত্রও এ সময় থেকে রচিত হয়। অষ্ট সাহসিক প্রজ্ঞা পারমিতা > প্রজ্ঞাপারমিতা হৃদয় সূত্র > প্রজ্ঞা পারমিতা ধারণী > প্রজ্ঞাপারমিতা মন্ত্ররূপ সংক্ষেপকরণ পরম্পরায় অবশেষে প্রং এই বীজমন্ত্রে (তুলনীয় ওঁ) রূপ নিয়েছে। এই মন্ত্রনির্ভর পূজা-ধ্যান পদ্ধতির নাম মন্ত্রযান। সম্ভবত: এই মন্ত্রতত্ত্বের সঙ্গে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের যোগাচার পদ্ধতির মিশ্রণ ঘটে। আর প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্ব এর দার্শনিক ভিত্তি হয়। তার থেকেই ক্রমে বিভিন্ন মতের উদ্ভব হয়ে পাল আমলে তিনটি বিশিষ্ট উপমত হিসেবে বিকাশ লাভ করে। এ তিনটি হচ্ছে : বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান।
নাগার্জুনের মতে শূন্যতাই হচ্ছে নির্বাণ। এ মত পরে বসুবন্ধুরও সমর্থন পায়। তিনি বলেন, গ্রাহ্য-গ্রাহকের অস্তিত্বহীনতাই শূন্যতা আর এই শূন্যতাই নির্বাণ। অর্থাৎ বাহ্যত সবকিছু থাকা সত্ত্বেও পারমার্থিক দৃষ্টিতে সব মায়ামাত্ৰভ্ৰমস্বরূপ–এটি অবিদ্যাজাত।
বজ্রযান
বজ্রযানে এই শূন্যতার নাম বজ্র। এটি অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অদাহী, অবিনাশী বজ্র। এই তত্ত্বই বজ্রসত্ত্ব–তার প্রমূর্তরূপ আদিবুদ্ধ। তিনিই পরমদেবতা। এই পরমদেবতা আত্মাও বটে, আবার সর্বজনীন পরমসত্তারূপে পরমাত্মাও বটে। এ বোধ মূলত ঔপনিষদিক এবং আস্তিক্যসূচক। এই বজ্রসত্ত্ব পরমব্রহ্মের মতো নির্গুণ, আবার সগুণও বটে। এই হচ্ছে বোধিচিত্ত বা শূন্যতা ও করুণা জ্ঞানরূপ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ অবস্থা।
বৌদ্ধ ধর্মচক্র বা ধর্মকায় বজ্রযানে বজ্রকায়রূপে অভিহিত হয়। এই বজ্রকায় বজ্রসত্ত্বস্বরূপ এবং জ্ঞান ও করুণারূপ বুদ্ধ। এই আদি বুদ্ধের পঞ্চগুণ–রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান। এদের নাম পঞ্চস্কন্ধ। এই পঞ্চস্কন্ধের প্রতীক দেবতা হচ্ছেন–বৈবোচন, রত্নসম্ভব, অমিতাভ, আমোঘসিদ্ধি ও অক্ষোভ্য। উক্ত সব স্কন্ধের ধ্যানের প্রয়োজনে সৃষ্ট বলে দেবতারা ধ্যানী বুদ্ধ বলে অভিহিত হন। এঁদের প্রকৃতি বা শক্তি হচ্ছেন যথাক্রমে তারা (বজ্রধাত্বেশ্বরী) মামকী, পাণ্ডরা, আর্যরা বা তারা ও লোচনা। এঁদের বোধিসত্ত্ব হচ্ছেন চক্রপাণি (সমন্তন্দ্র), রত্নপাণি, পদ্মপাণি (অবলোকিতেশ্বর), বিশ্বপাণি ও বজ্ৰপাণি। এরা ভূতপিশাচদেরও নাকি পূজা করত। যোনি প্রতীক যন্ত্রপূজাও করত।
দেবীদের মধ্যে আর্যরা–শ্যামাতারা, শেততারা, উগ্রতারা প্রভৃতি নানা নামে বিশেষ জনপ্রিয় হন। তাছাড়া হারিতা, মারীচি প্রভৃতি নামের প্রকৃতিও পরিকল্পিত হয়েছে। এই তারা পরে হিন্দু কালিকাতে রূপান্তরিত হয়েছেন। বৌদ্ধতন্ত্রে বজ্রসত্ত্ব হচ্ছে হেরুক বা হে বস্ত্র এবং তাঁর প্রকৃতির নাম হচ্ছে বজসত্ত্বাত্মিকা, বজ্রবরাহী, প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞা পারমিতা প্রভৃতি আর তার আবাহনের বীজমন্ত্র হল হুং। শূন্যতা ও করুণাকে কমল (প্রজ্ঞা), বজ্র (পুরুষ), প্রজ্ঞা (নারী), উপায় (পুরুষ), চন্দ্র (নারী), সূর্য (পুরুষ), এবং পুরুষ ও প্রকৃতিরূপেও কল্পনা করা হয়েছে। এ দুটোর মিলনজনিত এক তুরীয় আনন্দময় অবস্থা বা চেতনার নাম বোধিচিত্ত। এইটিই তান্ত্রিকতত্ত্ব। শৈব-শাক্ত তন্ত্রের সঙ্গে এখানেই বৌদ্ধতন্ত্রের মৌলিক ঐক্য। বোধিচিত্তেই মহাসুখ, কমলকে (প্রজ্ঞা তথা নারী) বৌদ্ধতন্ত্রে (যোনির) এবং বজ্রকে (উপায় তথা পুরুষ) পুংলিঙ্গের প্রতীকরূপে ধরা হয়েছে! তাই বজ্ৰকমল সংযোগ অর্থ মৈথুনক্রিয়া। এই মৈথুনে যে সামরস্য তাই যুগনদ্ধ বা অদ্বয় এবং এই সামরস্যজাত আনন্দাবস্থাই বোধিচিত্ত। [এতদ অদ্বয়ং ইতি উক্তং বোধিচিত্তং ইদম পরম– সাধনমালা, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭] অতএব প্রজ্ঞা-উপায় মৈথুনজাত মহাসুখরূপ বোধিচিত্ত লাভ করাই এ সাধনার লক্ষ্য। এ বজ্ৰতন্ত্রে হে বজ্র (বজ্রসত্ত্ব) নারী যোনিতে শুক্ররূপে বাস করেন বলে এবং শুক্র বিনা মহাসুখ লাভ সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন। বজ্রযানীরা চর্যাগীতির মতো বগীতিতে তাদের সাধনতত্ত্ব ব্যক্ত করত। উল্লেখ্য যে আদিকাল থেকেই গানের মাধ্যমে সাধন-ভজন রীতি চালু রয়েছে। সব ধর্মেই গান কৃচিৎ নাচ] সাধনা ও উপাসনার প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ অঙ্গ।
কালচক্রযান
বজ্রযানের সঙ্গে কালচক্রযানের মৌলিক কোনো তফাৎ নেই। কালচক্রযানে কালচক্রই বজ্রসত্ত্ব। অর্থাৎ এখানে কাল-এর উপরই অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কেননা কাল ঘসতি ভূতানি। কালচক্র হচ্ছে–শূন্যতা ও করুণার তথা প্রজ্ঞা-উপায়ের অদ্বয়সত্তা। কালকে জয় বা অতিক্রম করে চিরন্তন বোধিচিত্ত লাভ তথা জন্ম ও মৃত্যু (উৎপত্তি ও ক্ষয়) নিরোধক শক্তিলাভই এ সাধনার লক্ষ্য। তাই কালচক্র বুদ্ধের জনকস্বরূপ এবং ত্রিকাল ও ত্রিকায়ের ধারক। (বিমলপ্রভা-বাংলার বাউল ও বাউল গান গ্রন্থের পাদটীকায় উদ্ধৃত। পৃষ্ঠা ২৩৪-৩৫)। সাধন সম্বন্ধে কালচক্রযানীরা দিন, তিথি, নক্ষত্র, যোগ প্রভৃতির বিচার করিতেন বলিয়া মনে হয়। অভয়াকর গুপ্ত কালচক্রাবতার গ্রন্থে বার তিথি-নক্ষত্র-যোগ-করণ-রাশি-ক্ষেত্রি-সংক্রান্তি প্রভৃতির বিশদ আলোচনা করেন। এ কথা সঙ্গতভাবেই অনুমান করা যায় যে, কালচক্রপন্থী সাধকেরা গ্রহ-নক্ষত্রের গতি অনুসারে তাহাদের সাধনজীবন নিয়ন্ত্রিত করিতে চেষ্টা করিতেন।৩৪ বৌদ্ধতন্ত্রে–বজ্র ও কালচক্রানে–তুকতাক্ উচাটন-বশীকরণ-মারণ প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিক আচারাদি ছিল।
সহজযান
সহজযান দেব-দেবী, পূজা, মন্ত্র, প্রভৃতি সর্বপ্রকার আনুষ্ঠানিক ও আচারিক ধর্মের বিরোধী। কিন্তু বজ্রযানের সাধনপদ্ধতি ও সহজ যানের সাধনপদ্ধতি অভিন্ন। এমনকি বজ্রধর বা বজ্রসত্ত্বকে তারা মানে। সহজযানের প্রসারক্ষেত্র নেপাল ও তিব্বত। এ মার্গের শাস্ত্রগ্রন্থগুলোও তাই তিব্বতী ভাষায় অনূদিত ও রক্ষিত। আমাদের দোহাকোষ ও চর্যাপদগুলো সহজযানী সিদ্ধাদের রচিত। চর্যাপদে বামাচার ও প্রকৃতিবর্জিত সাধনার মিশ্রণ আছে। সহজযান মতেও প্রজ্ঞা-উপায়ের মিলনজনিত সামরস্য থেকেই মহাসুখরূপ সহজের উদ্ভব। এটিই বোধিচিত্ত। বৌদ্ধ চৌরাশী সিদ্ধার সবাই সহজিয়া ছিলেন না। তার প্রমাণ গোরক্ষ-মীননাথ কাহিনী–এঁরা প্রকৃতিবর্জিত পরম যোগী। কেউ কেউ সহজিয়া ছিলেন, তা চর্যাগীতিতে লক্ষণীয়।
সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও আচার প্রতিষ্ঠার জন্যে রাজকীয় প্রয়াস চলে। এ সময়েই কালবিবেক, দায়ভাগ প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থাল্লেখিত ব্রাহ্মণ্য আচার সমাজে বহুল প্রচলিত হয়। বারো মাসে তেরো পার্বণের শুরু হয় এভাবেই। চর্যাপদ থেকে এমনও অনুমান করা যায় যে, এ সমস্ত সহজযানীদের মধ্যে দ্বিবিধ সাধনপদ্ধতি চালু ছিল; একটি মৈথুনাত্মক তান্ত্রিকপদ্ধতি, অপরটি প্রকৃতিবর্জিত–বিশুদ্ধ যোগ-প্রণালী, হঠযোগের (চন্দ্র+সূর্য) মাধ্যমে দেহ বা কায়াসাধনই ছিল এঁদের লক্ষ্য।
বিন্দুধারণ ও ঊর্ধে সঞ্চালন করে সহস্রার মধ্যে নিয়ে সচ্চিদানন্দ রূপ মহাসুখ ও সহজানন্দ এর অবস্থা সৃষ্টি করাই লক্ষ্য। এটিই নির্বাণানন্দ তথা শূন্যতা।
নাথধর্ম :
বলেছি, সেন আমলে ব্রাহ্মণ্যবাদ রাজধর্মরূপে গৃহীত হয়। ফলে বিভিন্ন ও বিভক্ত বৌদ্ধ সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে পড়ে। বিশেষ করে, স্মৃতির বিধান-অনুগ সমাজ ও শাসনব্যবস্থা চালু হওয়ায় লোকজীবনে সে-প্রভাব এড়ানো সম্ভব হয়নি। সেনদের রক্ষণশীলতা আর অনুদারতাও বৌদ্ধ বিলুপ্তির জন্যে অংশত দায়ী। এ বিরুদ্ধ পরিবেশে কোনো কোনো বৌদ্ধ সম্প্রদায় কিছু হিন্দু-দেবতা ও আচার গ্রহণ করে হিন্দুয়ানীর আবরণে পৈত্রিক ধর্ম বাঁচিয়ে রাখার প্রয়াসী হয়। এরূপে এক যোগী তান্ত্রিক বৌদ্ধ সম্প্রদায় প্রজ্ঞা-উপায়ের পরিবর্তে শিব-উমা নাম দিয়ে নিজেদের প্রাচীন বিশ্বাস সংস্কার চালু রাখে। মীননাথ-গোরক্ষনাথ-হাড়িপা-কানুপা প্রভৃতি এই সম্প্রদায়ভুক্ত। মীননাথ গোরক্ষনাথের নাম অনুসারেই এ সম্প্রদায় নাথপন্থীরূপে আমাদের কাছে পরিচিত। বৌদ্ধ সহজিয়ারা ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবের কালে দুটো ভিন্ন পথে রূপান্তর লাভ করে : বামাচার বর্জিত যোগীরা শৈবনাথরূপে এবং কামাচারীরা বৈষ্ণব সহজিয়া রূপে হিন্দু সমাজের উপসম্প্রদায়ে পরিণত হয়। দ্রাবিড় দেবতা শিব ও উমাকে৫ অনেক আগেই ব্রাহ্মণ্যবাদীরা পুরুষ-প্রকৃতির বিগ্রহরূপে গ্রহণ করেছিল, পরে শৈব-শাক্ততন্ত্রের শিব-উমাই (বা গৌরী) অবলম্বন হয়। তেমনি বৌদ্ধরাও পুরুষ প্রকৃতিকে প্রজ্ঞা-উপায় রূপে কল্পনা করে। আবার বৌদ্ধ বিলুপ্তিকালে প্রজ্ঞা-উপায়ের প্রতীকী পরিবর্তনে রাধাকৃষ্ণ তথা বিষ্ণু-লক্ষ্মী আরাধ্য হয়ে উঠেন। এ কারণে এ সম্প্রদায় বৈষ্ণব সহজিয়া নামে এক উপসম্প্রদায় হিসেবে হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বিষ্ণু ও তাঁর অবতার কৃষ্ণ মহাভারতীয় যুগ থেকেই উত্তরভারতিক ধর্মে প্রাধান্য পেয়েছেন। নাথপন্থ যে বৌদ্ধ সহজিয়া মতবাদ থেকে উদ্ভূত তা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, সুশীল কুমার দে প্রমুখ স্বীকার করেছেন। অবশ্য শশিভূষণ দাশগুপ্ত ও কল্যাণী মল্লিকের মতে নাথপন্থ একটি প্রাচীন শৈবমত। কিন্তু ডক্টর মল্লিক বৌদ্ধ সহজযানের সঙ্গে এর সাদৃশ্যও স্বীকার করেছেন–নাথমার্গে হিন্দুর তন্ত্র ও বৌদ্ধ সহজিয়াদের রহস্যবাদের অপূর্ব মিশ্রণ আছে। নাথ হঠযোগ ও বৌদ্ধসহজিয়া সাধনার সাধ্য আছে। …. নাথ ধর্মকে হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধ যোগ-তত্ত্বের সংমিশ্রণ বলা যাইতে পারে। আসলে প্রজ্ঞা-উপায়ের পরিবর্তে শিবশক্তির প্রতীকীরূপে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েই ডক্টর মল্লিক–হিন্দুতন্ত্র, সহজিয়ামত ও নাথপন্থে নানা সাদৃশ্য লক্ষ্য করেও–নাথমার্গকে শৈবমত বলেছেন। নাথেরা যে ব্রাহ্মণ্য শৈব নয়, তার একটি প্রমাণ নাথেরা শূন্যবাদী ও কায়াসাধুব্রতী। আর ব্রাহ্মণ্য আদিনাথ শিব আদিবুদ্ধেরই প্রতিশব্দের মতো। নাথদের এক পীঠস্থান কামাখ্যা। কদলিনগরও নাকি কামরূপে। নাহযোগী সম্প্রদায় (তাঁতিরা) তাদের সমাজ, আচার, পূজাপদ্ধতি ও সঙ্কারাদি আজো স্বতন্ত্রভাবে রক্ষা ও পালন করে। এরা প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ। অবশ্য বৌদ্ধ বিলুপ্তির ফলে এরা হিন্দু-শৈবযোগীদের প্রভাবে পড়েছে। ভৈরব নামে শিবপূজা তার অন্যতম। নাথপন্থী সাধকরাও নানা মতগত সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তারা যোগী, গোরক্ষনাথী, দর্শনী, কানফাটা, সিদ্ধ ইত্যাদি নামে পরিচিত। এখন এসব উপসম্প্রদায়ের কেউ শাক্ত, কেউ শৈব, কেউ বা (বৌদ্ধ) যোগী। তাই এদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে দুর্গাপূজা, চক্রপূজা, যযানি ও লিঙ্গপূজা, শ্ৰীযন্ত্রপূজা প্রভৃতি চালু রয়েছে। বৌদ্ধ ঐতিহ্য রয়েছে বলেই শক্তিকে এরা মাতৃকা জ্ঞান করে না। বৌদ্ধতন্ত্রের অষ্টসিদ্ধির অন্তর্ধান খেচর প্রভৃতি সিদ্ধি আমরা মীননাথ গোরক্ষনাথ ও হাড়িপা কাহিনীর মধ্যে পাই। মারণবশীকরণ–উচাটন–জ্যোতিষী প্রভৃতি ঐন্দ্রজালিক আচার-সিদ্ধিও নাথপন্থর লক্ষ্য ছিল। নাথমার্গেও শূন্যবাদ আছে। শৈব ব্যোমবাদ আকাশ, পরাকাশ, মহাকাশ, তত্ত্বাকাশ ও সূর্যাকাশ বৌদ্ধ সহজযানীদের শূন্য, অতিশূন্য ও সর্বশূন্যের তুল্য। শূন্য ও বধিচিত্ত এবং নির্গুণ তুরীয় অবস্থা একই। এ-ই নির্বাণ।
বৈষ্ণব সহজিয়া :
বলেছি, বৌদ্ধ-বিলুপ্তির পর বাঙালি বৌদ্ধসম্প্রদায় হিন্দু-সমাজে মিশে গিয়ে হিন্দুয়ানীর আবরণে তাদের মতাবলী প্রচ্ছন্ন রেখেছিল। বৈষ্ণব সহজিয়া, ধর্মপূজারী, নাথযোগী, হিন্দুতান্ত্রিক প্রভৃতির উদ্ভব এভাবেই হয়েছে। বৌদ্ধ সহজিয়ার সঙ্গে বৈষ্ণব সহজিয়ার পার্থক্য বিশেষ কিছুই নেই। কেবল শূন্যতত্ত্ব বা নির্বাণ বা বোধিচিত্তের স্থলে মহাভাব রূপ সহজ তথা পরমানন্দ এবং প্রজ্ঞা উপায়ের পরিবর্তে রাধা-কৃষ্ণ নামই পার্থক্য সূচিত করেছে। এ কারণে পরকীয়া নারী-মৈথুন, বিন্দুধারণ ও ঊর্ধ্বে সঞ্চালন এবং রাগানুগা সাধনা প্রভৃতি প্রক্রিয়ার নামান্তর ঘটেছে। বৌদ্ধদের মতো এরাও বেদ-বিরোধী। বৌদ্ধদের মতো এরাও একান্তভাবে গুরুবাদী। সৎগুরুর কাছে দীক্ষিত
হয়ে কেউ মহাভাব বা সহজ-এর অধিকারী হতে পারে না। এভাবে হিন্দুতান্ত্রিক ধর্মও গড়ে উঠেছে বৌদ্ধতন্ত্রের কোনো কোনো পরিভাষা ও পদ্ধতির রূপান্তরে ও তত্ত্বের কলেবর বৃদ্ধিতে। বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধ ও হিন্দু মূর্তি-শিল্পে তার সাক্ষ্য রয়েছে। তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনাকে বজায় রেখে যারা বৈষ্ণব ধর্মের আশ্রয় নিয়েছিল, তারাই বৈষ্ণব সহজিয়া। তারাই অন্য লোকের চোখে নেড়ানেড়ী। নেড়ানেড়ী কথাটিও বৌদ্ধ ঐতিহ্যের ইঙ্গিতবাহী মুণ্ডিত মুখ ও মস্তক]। কেবল রাধাকৃষ্ণ রূপকের মধ্যে (তথা পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বের মধ্যে) যারা সাধন ভজন আবদ্ধ রেখেছে, তারাই বৈষ্ণব সহজিয়া। আর যারা নির্বিচারে নানা রূপক ও প্রভাব গ্রহণ করেছে, তারাই বাউল। দুইয়ের পার্থক্য এ-ই।
বাউল :
বাউলদের জনশ্রুতিজাত ধারণা, স্বয়ং চৈতন্যদেবের একটি গুহ্য সাধনপ্রণালী ছিল। এই সাধনা ছিল পরকীয়া মৈথুনাত্মক। রূপ, সনাতন, নিত্যানন্দ, জীব প্রমুখ বৈষ্ণব সাধকগণের পরকীয়া সঙ্গিনী ছিল। চৈতন্যদেব স্বয়ং মুসলমান আউলচাঁদ রূপে পুনরাবির্ভূত হয়ে এই সাধনপ্রণালী সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। আউলচাঁদের পুত্র রাম শরণ, তাঁর পুত্র দুলাল চাঁদ কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা বলে লোকশ্রুতি আছে। সম্ভবত আউলচাঁদের শিষ্যা মাধববিবি এবং মাধববিবির শিষ্য নিত্যানন্দ পুত্র বীরদ্র ও বীরচন্দ্র এই সাধনতত্ত্ব জনপ্রিয় করেন। আউলাদ ফকির ঠাকুর নামে খ্যাত এবং কর্তাভজা মতের আদি গুরু বলে পরিচিত। বাউলেরা প্রায়ই অশিক্ষিত। বাউলদের লিখিত শাস্ত্র, ইতিহাস বা দর্শন নেই। তাই তারা কোনো প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারে না। এজন্যেই পরোক্ষ তথ্যের আলোকে অনেকটা অনুমান-নির্ভর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়।
না বললেও চলে যে রাধাকৃষ্ণ নামের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে রাধাকৃষ্ণের যুগলাবতার চৈতন্যদেবকে বাউল মতের উদ্ভাবকরূপে প্রচার করে তারা এই সাধনতত্ত্বকে শ্রদ্ধেয় করার এবং আভিজাত্য দানের প্রয়াস পেয়েছিল। আসলে তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনাকে বজায় রেখে যারা বৈষ্ণবধর্মের আশ্রয় নিয়েছিল তারাই বৈষ্ণব সহজিয়া বা রসিক বৈষ্ণব। প্রজ্ঞা-উপায়ের পরিবর্তে রাধাকৃষ্ণ প্রতাঁকে সাধনা চৈতন্য-পূর্ব যুগেই হয়তো শুরু হয়েছিল, কিন্তু চৈতন্যোত্তর কালেই এ সম্প্রদায়ের প্রকাশ্য প্রসার ঘটে। তারই একটি শাখার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আউলচাঁদ। আর অপর শাখার প্রবর্তক ছিলেন মাধববিবি। এই শাখার বিস্তৃতি ঘটে সম্ভবত বীরভদ্রের চেষ্টায়। এটিরই লোক-প্রচলিত নাম বাউল সম্প্রদায়। যেসব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ইসলাম কবুল করেছিলেন আর যেসব প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ হিন্দুসমাজ ভুক্ত হয়ে নিজেদের পূর্বপুরুষের ধর্মাচরণে রত ছিল, তারাই কালে বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছে। বৌদ্ধ-ঐতিহ্যের সাধারণ উত্তরাধিকার ছিল বলেই হিন্দু-মুসলমানের মিলনে বাউল মত গড়ে উঠতে পেরেছে।
হিন্দুপ্রভাবে বাউল গানে রাধাকৃষ্ণ, শিব-শিবানী, মায়া-ব্রহ্ম, বিষ্ণু-লক্ষ্মী প্রভৃতি পুরুষ-প্রকৃতির প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। মুসলিম প্রভাবে তেমনি মোকাম, মঞ্জিল, লতিফা, সিরাজম্মুনিরা, আল্লাহ, কাদের, গনি, রসুল, রুই, আনল হক, আদম-হাওয়া, মুহম্মদ-খাদিজা, আলি-ফাতেমা প্রভৃতি প্রতীকী রূপক গৃহীত হয়েছে। আবার বৌদ্ধনাথ এবং নিরঞ্জনও পরিত্যক্ত হয়নি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পৌরাণিক উপমা ও কুরআন হাদীসের বাণীর নানা ইঙ্গিত (যেমন বর্জখ]। অবশ্য বাউল রচনায় এসব শব্দ ও পরিভাষা তাদের মতানুগ অর্থান্তর তথা নতুন ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। বৈষ্ণব ও সুফী সাধনার সঙ্গে বাউল মতের মৌলিক পার্থক্য বর্তমান। সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি পরিহার করে যে-মিলন-ময়দান তারা তৈরি করল, তাকে সার্থক ও স্থায়ী করার জন্যে পরমাত্মা বা উপাস্যের নামেরও এক সর্বজনীন পরিভাষা তারা সৃষ্টি করেছে। তাদের ভাষায় পরম তত্ত্ব পরমেশ্বর বা সচ্চিদানন্দ হচ্ছে মানুষ, অটল মানুষ, সহজ মানুষ, অধর মানুষ, রসের মানুষ, ভাবের মানুষ, অলখ সাই (অলক্ষ্য স্বামী), অচিন পাখী, মনুরা (মনোরায়, মনোরাজা) প্রভৃতি পরমাত্মা আত্মারই পূর্ণাঙ্গরূপ। দেহস্থিত আত্মাকে কিংবা আত্মা সম্বলিত নরদেহকে যখন মানুষ বলে অভিহিত করি, তখন পূর্ণাঙ্গ বা অখণ্ড আত্মা বা পরমাত্মাকে মানুষ বলতে বাধা কী?
বাউলেরা বৈধি তথা বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য আচার বিরোধী এবং মৈথুনাত্মক পরকীয়া ও রাগানুগা সাধনার পক্ষপাতী। বাউল মতবাদও ভোগমোক্ষবাদ। শিবশক্তি, রাধাকৃষ্ণ ও পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব, সুফীমত ও নানা লৌকিক-তত্ত্বের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে বলে বাউল মতে অসঙ্গতিও কম নেই। তবু বাউলদের উপর বৈষ্ণব মতের (চৈতন্য চরিতামৃতের মাধ্যমে) এবং সুফীমতের (কলন্দরিয়া সম্প্রদায়ের মাধ্যমে) প্রভাবই অত্যধিক। ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে সতেরো শতকের মধ্যভাগ থেকেই বাউল মতের উদ্ভব। গুরু, মৈথুন ও যোগ–তিনটিই সমগুরুত্ব পেয়েছে বাউল মতে। তাই গুরু, বিন্দুধারণ ও দম বা শ্বাস-প্রশ্বাসের কথা বাউল গানে অত্যধিক। সগুরুর কাছে। দীক্ষা না নিলে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করা অসম্ভব এবং বিন্দুধারণে সামর্থ্যই সিদ্ধির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। বাউলমতে আত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন অর্থাৎ আত্মা পরমাত্মার অংশ। আত্মাকে জানলে পরমাত্মাকেই জানা হয়। এই দেহস্থিত আত্মাই মানুষ, মনের মানুষ, রসের মানুষ, ভাবের মানুষ, অলখ সই। বাউলের রসস্বরূপ হচ্ছে সাকার দেহের মধ্যে নিরাকার আনন্দস্বরূপ আত্মাকে স্বরূপে উপলব্ধি করার প্রয়াস। এটিই অটলমানুষ তথা আত্মতত্ত্ব। এ হচ্ছে অরূপের কামনায় রূপসাগরে ডুব দেয়া, স্বভাব থেকে ভাবে উত্তরণ। সহজিয়াদের সহজই সহজ মানুষ। মৈথুন মাধ্যমে বিন্দুধারণ ও উর্ধ্বে সঞ্চালনের সময়ে গঙ্গা (ইড়া) ও যমুনা (পিঙ্গলা) বেয়ে সরস্বতীতে (সুষুম্নায়) ত্রিবেণী (মিলন) ঘটাতে হয়। তারপর সেখান থেকে সহস্রায় (মস্তকস্থিত-সহস্রদল পদ্মে) যখন বিন্দু গিয়ে পড়ে, তখনই সৃষ্টি হয় মহাভাব বা সহজ অবস্থা। মুলাধারের রজঃকে ফুল, শত্রুকে ক্ষীর ও নিঃসৃত রজঃকে নীর বলে। এই রজো-বীজে বা নীর-ক্ষীরেই মিশে রয়েছে সহজ মানুষ। বৌদ্ধ মতে হেবজ্র (বজ্রসত্ত্ব) শুক্ররূপে নারী-যোনিতে বাস করেন। সহজিয়াদের মতেও ধাতুরূপে সর্বদেহে বৈসে কৃষ্ণশক্তি [বিবর্ত বিলাস–অকিঞ্চন দাস]। এজন্যে পুরুষ নারীরজ : এবং নারী পুরুষের শুক্র পান করে। সাধনার দ্বারা সহজ মানুষের বা মহাচৈতন্যের তথা আত্মার অবিমিশ্র সত্তাবোধ জাগাতে হয়। মৈথুন পদ্ধতিই রাগানুগ পদ্ধতি। চারিচন্দ্র হচ্ছে–মল, মূত্র, রজ : ও শুক্র। এসবের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও আছে। রস বলতেও উক্ত চারি পদার্থকে বোঝায়, আবার সাধারণভাবে প্রেম বা শৃঙ্গার রসও নির্দেশ করে। বাণ পুরুষশক্তি এবং গুণ প্রকৃতি-শক্তি।
বাউলদের মনের মানুষ, মনুরা, সহজমানুষ, অধরমানুষ, ভাবের মানুষ বা অলখ সাঁই-এর সঙ্গে আদিবুদ্ধ, আদিনাথ, বোধিচিত্ত ও সচ্চিদানন্দতত্ত্বের মৌলিক ঐক্য রয়েছে। বৈষ্ণব-সহজিয়াদের সঙ্গে হিন্দু-বাউলের অনেক ব্যাপারেই সাদৃশ্য রয়েছে। বিভিন্ন গুরুর মত বা নামানুসারে এরা বিভিন্ন উপসম্প্রদায়ে বা সমাজে বিভক্ত, যথা কর্তাভজা, কিশোরীভজা, বলরামী, শম্ভচাদী প্রভৃতি। মুসলমান বাউলরা নেড়ার ফকির, আউল, সই, সাহেব ধনী, হযরতী, দরবেশ প্রভৃতি নামে পরিচিত ও বিভিন্ন গুরুপন্থী সমাজে বিভক্ত। দেহ নিরপেক্ষ আত্মার স্থিতি সম্ভব নয়, কাজেই দেহাধারেই আত্মাকে খুঁজতে হবে। এই ধারণা দেহতত্ত্বে আগ্রহ জাগিয়েছে। ফলে দেহের চর্যা ও দেহ-সম্বন্ধীয় তথ্য উদঘাটন আবশ্যিক হয়েছে। বৌদ্ধ-তান্ত্রিকদের আমল থেকে দেহ ও সাধনা সম্বন্ধীয় যেসব পরিভাষা ব্যবহৃত হয়ে আসছে, সেগুলোর একটি তালিকা দিচ্ছি। এতে দেহের বাম ও দক্ষিণের একটি স্কুল পরিচয় মিলবে :
দেহের দক্ষিণাংশে : রসনা, পিঙ্গলা, সূর্য, রবি, অগ্নি, প্রাণ, চমন, কালি, বিন্দু, উপায়, যমুনা, রক্ত, পলিতা, সূক্ষ্ম, রেত :, ধর্ম, স্থির, পর, দ্যৌ, ভেদ, চিত্ত, বিদ্যা, রজ:, ভাব, পুরুষ, শিব, জিনপুর, নির্মাণকায়, গ্রাহ্য ও গগন।
দেহের বামাংশে : ললনা, ইড়া, চন্দ্র, শশী, সোম, আপান, ধমন, আলি, নাদ, প্রজ্ঞা, গঙ্গা, শুক্র, বলি, স্কুল, রজ:, অধম, অস্থির, অপর, পৃথিবী, অভেদ, অচিত্ত, অবিদ্যা, তামস, অভাব, প্রকৃতি, শক্তি, সম্ভোগকায় ও গ্রাহক।
অবশ্য এসব পরিভাষার সবগুলো বাউল সাধনায় ও বাউল রচনায় মিলবে না। কারণ কালে অনেকগুলোর গূঢ়ার্থের স্মৃতি লোকমানস থেকে মুছে গেছে। বিভিন্ন ধর্মতত্ত্বের ও সাধন-প্রণালীর প্রভাবে পড়েছে বলে বাউল সাধনায় কোনো একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসৃত হয় না। এজন্যে মুসলমান বাউলদের মধ্যে পরকীয়া ও মৈথুনাত্মক সাধনা দুর্লক্ষ্য; তারা যৌগিক প্রক্রিয়ায় শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণকেই প্রাধান্য দেয়।
বিভিন্ন মতবাদের মিশ্রণে গড়ে উঠেছে বাউল মত। হিন্দু-মুসলমানের মিলনে হয়েছে বাউল সম্প্রদায়। তাই পরমতসহিষ্ণুতা, অসাম্প্রদায়িকতা, গ্রহণশীলতা, বোধের বিচিত্রতা, মনের ব্যাপকতা ও উদার সদাশয়তা এদের বৈশিষ্ট্য।
নানা বরণ গাভীরে ভাই
একই বরণ দুধ
জগৎ ভরমিয়া দেখিলাম
একই মায়ের পুত।
মানুষ নির্বিশেষকে এমন উদারদৃষ্টিতে দেখা যে-জীবনবোধের দ্বারা সম্ভব, তার উৎস যে ধর্মমত বা মরমিয়াবাদ তা কখনো তুচ্ছ হতে পারে না। মুসলমান বাউলের হিন্দুগুরু, হিন্দু বাউলের মুসলমানগুরু এমন প্রায়ই দেখা যায়।
সাধারণ দৃষ্টিতে মুসলমান বাউলেরা আধা-মুসলমান। এরাই বাঙলা দেশে মুসলমানের সংখ্যা বাড়িয়েছে। সূফী-দরবেশরা তাদের এমনি আধা-মুসলমান করে না রাখলে, সরাসরি শরীয়তী ইসলাম প্রচারে এত লোককে দীক্ষিত করা যেত না হয়তো। আগে নামত মুসলমান সমাজভুক্ত ছিল বলেই উনিশ-বিশ শতকে তাদের অধিকাংশকে সহজেই পুরো মুসলমান করা সম্ভব হয়েছে।
বর্তমানে বাঙলাদেশে প্রায় তিন লক্ষের মতো বাউল রয়েছে। ওয়াহাবী-ফরায়েজী ও আহলে হাদীস আন্দোলনের ফলে মুসলমান বাউলের অনেকে উনিশ-বিশ শতকে শরীয়তী ইসলামে ফিরে এসেছে, তেমনি ইংরেজি শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু বাউল-সন্তানও ব্রাহ্মণ্য আচার বরণ করেছে। নইলে বাঙলার বিশেষ করে মধ্য, উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের, এককথায় পদ্মার ওপারের নিম্নশ্রেণীর বাঙালির মধ্যে বাউলের সংখ্যা নগণ্য ছিল না।
বাউলধর্মে বৈরাগ্য নেই। বাউলেরা মুখ্যত তাত্ত্বিক, গৌণত প্রেমিক। এই তাত্ত্বিকতা অনেককেই বিষয়ে অনাসক্ত রাখে। তাই বাউল দুই প্রকার : গৃহী (বিষয়ী গৃহী) ও বৈরাগী (অনাসক্ত গৃহী)। বাউল বৈরাগীরা সাধারণত ভিক্ষাজীবী। বাউল মত বাঙলার ধর্ম, বাঙালির ধর্ম, একান্তভাবেই বাঙালির মানস ফসল। দেশী ভাবে ও বিদেশী প্রভাবে এর উদ্ভব। সমাজের উপরতলার লোকের ধর্ম হলে এই মতবাদ যে কেবল বাঙালির জীবন ও ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করত তা নয়, দুনিয়ার মানুষের কাছে উদার মানবিকতার জন্যে বাঙালিকে শ্রদ্ধেয়ও করে তুলত।
বাউল নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিদ্বানদের মধ্যে মতভেদ আছে। নামটি বাউলদের স্বপ্রদত্ত নয়। পনেরো শতকের শেষপাদের শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের এবং ষোলো শতকের শেষপাদের চৈতন্যচরিতামৃতে ক্ষেপা ও বাহ্যজ্ঞানহীন অর্থে বাউল শব্দের আদি প্রয়োগ পাওয়া যায়। চৈতন্যদেবের কাছে প্রেরিত অদ্বৈতাচার্যের একটি হেঁয়ালিতেও বাউল শব্দের প্রয়োগ দেখেছি। রাঢ় অঞ্চলে এখনো বাউলকে ক্ষেপা বলে। কেউ বলেন বাউর (এলোমেলো, বিশৃঙ্খল, পাগল) থেকেই বাউল নামটির উৎপত্তি হয়েছে। অবশ্য উত্তরভারতের বাউরার সঙ্গে আমাদের বাউল-এর যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। তবু আকুল থেকে আউল এবং ব্যাকুল থেকে বাউল শব্দের উৎপত্তিও অসম্ভব নয়। আবার কেউ কেউ বলেন–এ মতের উদ্ভব যুগে দীন-দুঃখী, উলঝুল একতারা বাজিয়েদেরকে লোকে বাতুল বলে উপহাস করত। এ বাতুল শব্দ থেকে বাউল নামের উদ্ভব। কারুর কারুর মতে বায়ু শব্দের সঙ্গে স্বার্থে ল যুক্ত হয়ে, বায়ুভোজী উন্মাদ কিংবা শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ার দ্বারা সাধনাকারী অর্থে বাউল শব্দ তৈরি হয়েছে। ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বাউল শব্দটি আউল শব্দজ বলে মনে করতেন। তাঁর মতে, আউল আরবি আউলিয়া (ওলির বহুবচন) সস্তৃত। ডক্টর সৈয়দ আবদুল হালিমের মতে আউল শব্দটি আউয়াল শব্দজ। আগমের আরবি পরিভাষা হিসেবে আউয়াল শব্দটি গ্রহণ করে মুসলমান আগমতাত্ত্বিকেরা আউয়াল বা আউল নামে পরিচিত হয়। অবশ্য আগম-এর আরবি পরিভাষা আউয়াল-এর আউল রূপে বহুল প্রয়োগ বাউল গানে দেখা যায়। উপরোক্ত এ কয়টি ব্যাখ্যার কোনটাই উড়িয়ে দেবার মতো নয়। তবে ব্যাকুল বা বাতুল থেকেই বাউল নামের উদ্ভব বলে অনুমান করি। আমাদের এ অনুমানের পক্ষে একটি যুক্তি এই যে, সমাজের উঁচুস্তরে বাউলেরা কোনো কালেই শ্রদ্ধা বা মর্যাদার আসন পায়নি। তাই মনে হয়, ব্যাকুল (ভাবোন্মত্ত) কিংবা বাতুল (অপদার্থ) অর্থে উপহাসস্থলে তাদের এই নামকরণ হয়েছে। আর আউয়াল থেকে আউল শব্দের উদ্ভবের সম্ভাব্যতাও সহজে অস্বীকার করা যায় না। আবার বাউল মতের আদি প্রবর্তক বলে খ্যাত ব্যক্তির নামটিও আউলাদ। হয়তো আউয়ালবাদী (আগম-বাদী) বলেই তার নাম আউল চাঁদ। কিংবা গোড়ার দিকে আউল চাঁদের অনুসারীরাই ছিল আউল নামে পরিচিত।
সম্প্রতি অধ্যাপক এস. এম. লুৎফর রহমান তার বাউল শব্দের উৎপত্তি ও ব্যাখ্য নামের প্রবন্ধে৮ বাউল নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নতুন তথ্য দান করেছেন। তিনি অবহট্ট রচনায় ও চর্যাগীতিতে ব্যবহৃত বাজিল, বাজুল, বাজির, বাজ্জিল শব্দগুলোকে বাউল শব্দের পূর্বরূপ বলে নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে বজ্ৰী > বজ্জির > বাজির>বজ্জিল > বাজিল > বাজুল > বাউল। অবশ্য বজ্রযানী বৌদ্ধ যদি বজ্ৰকুল নামে অভিহিত হত বলে অনুমান করা সম্ভব হয়, তাহলে বজ্ৰকুল থেকে বাউল হওয়া আরো সহজ। যেমন বজ্রকুল > বজ্জউল > বাজুল > বাউল। যা হোক, বাউল যে বজ্রযানী নির্দেশক, সে সম্পর্কে আমাদেরকে নিঃসংশয় করার গৌরব অধ্যাপক লুৎফর রহমানের প্রাপ্য।
বাউল গান তাত্ত্বিক রচনা–তত্ত্বসাহিত্য। স্বল্পশিক্ষিত লোকের রচনা বলে এগুলো লোক সাহিত্যের উপর উঠতে পারেনি। বৈষ্ণবপদাবলী যেমন আঙ্গিক সৌষ্ঠবে, ভাবের সুষম অভিব্যক্তিতে, কাব্যরসে, শিল্পসৌন্দর্যে, ছন্দলালিত্যে ও সুচিত শব্দ-সম্পদে উকৃষ্ট কবিতার লাবণ্য লাভ করেছে, বাউল গান তেমন নয়। আঙ্গিকে, ছন্দে ও অভিব্যক্তির অসঙ্গতিতে ও শিল্পরুচির অভাবে এসব রচনা কবিতার পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি। অবশ্য ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। বিশেষ করে লালন, পাঞ্জ, হাউরে, মদন, যাদুবিন্দু প্রভৃতি কয়েকজনের রচনায় কাব্য-মাধুর্য দুর্লভ নয়। সাহিত্য হিসেবে বিচার করলে বাউল গান লালিত্য-বিরল লোকগীতিমাত্র, আর কিছু নয়। সুরের একঘেয়েমিও তত্ত্ব-বিমুখ শ্রোতার পক্ষে পীড়াদায়ক। বাউল গানের কদর আছে ভাবুক ও তত্ত্বপ্রিয় লোকের কাছে এবং তা গান হিসেবে নয়–তত্ত্বকথার আশ্রয় হিসেবে। বাউলেরা গানকে তত্ত্বপ্রচারের, ভজনের ও আত্মবোধনের কাজে লাগায়। গানের প্রথম চরণেই সাধারণত মূল বক্তব্যের আভাস মেলে এবং তার সৌন্দর্যও অবশ্য স্বীকার্য।
সব গুহ্য সাধনাই যোগ-নির্ভর। তাই এখানে যৌগিক সাধন প্রণালীর স্কুল পরিচয় দেয়া হল : দেহের মধ্যে রয়েছে অসংখ্য নাড়ি। তার মধ্যে তিনটে প্রধান–ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না; বা গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী। এ তিনটিকে মহানদী কল্পনা করলে অন্যসব হবে উপনদী বা স্রোতস্বিনী। এগুলো দিয়ে শুক্র রজ:, নীর-ক্ষীর-রক্ত প্রবহমান। এ প্রবাহ বায়ুচালিত। অতএব, বায়ু নিয়ন্ত্রণের শক্তি অর্জন করলেই দেহের উপর কর্তৃত্ব জন্মায়।
আবার শুক্র, রজঃ ও রক্ত হচ্ছে মিশ্রিত বিষামৃত–জীবনীশক্তি ও বিনাশ-বীজ, সৃষ্টি ও ধ্বংস, কাম ও প্রেম, রস ও রতি। শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের দ্বারা পবনকে নিয়ন্ত্রণ করলে গোটা দেহের উপরই কর্তৃত্ব জন্মায়। প্রশ্বাস হচ্ছে রেচক, শ্বাস হচ্ছে পূরক এবং দম অবরুদ্ধ করে রাখার নাম কুম্ভক। ইড়া নাড়িতে পূরক, পিঙ্গলায় রেচক করতে হয়। দম ধরে রাখার সময়ের দীর্ঘতাই সাধকের শ্রেষ্ঠত্বের লক্ষণ। এর নাম প্রাণায়াম।
ললাট-দেশে আছে সহস্রদল পদ্ম। নাম সহস্রার। মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনী শক্তির সঙ্গে এখানে পরমশিবের মিলন হয়। কুণ্ডলিনী হচ্ছে সাড়ে তিন চক্র করে থাকা মূলাধারস্থ সর্প। এটি রজ:বিষ বা কামবিষের প্রতীক। বিষকে অমৃতে পরিণত করে স্থায়ী আনন্দলাভ করাই সাধ্য।
এমনি অবস্থায় দেহ হয় ইচ্ছাধীন। এখন যে-শুক্রের স্থলনে নতুন জীবন সৃষ্টি হয়, সেই শুক্রকে নাড়িমাধ্যমে উধ্বে সঞ্চালিত করে তার পতন-স্খলন রোধ করলেই শক্তি সংরক্ষিত হয়। সেই সঞ্চিত শুক্র শরীরে জোয়ারের মতো ইচ্ছানুরূপ প্রবহমান রেখে স্থায়ী রমণ-সুখ অনুভব করাও সম্ভব।
যোগে সিদ্ধিলাভ হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি অর্জন। ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগে তখন মানুষ অসামান্য শক্তির অধিকারী হয়ে অসাধ্য সাধন করে। শুক্র থাকে লিঙ্গের কাছে। সেটাকে প্রজনন শক্তির প্রতীক সর্পস্বরূপ মনে করা হয়েছে। কুণ্ডলীকৃত সুপ্ত সর্পের কল্পনাই কুণ্ডলিনী নাম পেয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে কাম বিষ। কাম বিষ-রূপ সৃষ্টিশীল শুক্র স্থলনেই সৃষ্টি সম্ভব। শুক্রই জীবনীশক্তি। কাজেই সৃষ্টির পথ রোধ করা দরকার। ফলে শক্তি ব্যয় হবে না। আর শক্তি থাকলেই জীবনের বিনাশ নেই। মূলাধার থেকে তাই শুক্রকে নাড়ির মাধ্যমে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করে ললাট-দেশে সঞ্চিত করে রাখলেই ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ প্রয়োেগ সম্ভব। এটিই সামরস্য, সহজাবস্থা, চিররমণানন্দাবস্থা বা সচ্চিদান্দাবস্থা–শিব-শক্তি, প্রজ্ঞা-উপায় বা রাধাকৃষ্ণের অন্বেয় সংস্থিতি। এটিই সিদ্ধি। আজকে যুক্তিপ্রবণ মনে এর একটি অনুমিত ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে এরূপ অস্বাভাবিক জীবনচর্যার ফলে একপ্রকার মাদকতা তাদের আচ্ছন্ন করে রাখে, আর তাতেই তারা হয়তো মনে করে যে তারা অতিমানবিক শক্তির অধিকারী হয়েছে এবং আত্মিক অমরত্ব লাভ ঘটেছে।
সাধনার তিনটে স্তর :১. প্রবর্ত, ২. সাধক ও ৩. সিদ্ধি।
১. প্রবর্তাবস্থায় যোগী সুষুম্নমুখে সঞ্চিত শুক্ররাশি ইমার্গে মস্তিষ্কে চালিত করার চেষ্টা পায়। এতে সাফল্য ঘটলে যোগী প্রেমের করুণারূপ অমৃতধারায় স্নাত হয়।
২. শৃঙ্গারের রতি স্থির করলে তথা বিন্দুধারণে সমর্থ হলে যোগী সাধক নামে অভিহিত হয়। তখন মস্তিষ্কে সঞ্চিত শুক্ররাশিকে পিঙ্গলা পথে চালিত করে সুষুম্নমুখে আনে। ফলে বিন্দু আজ্ঞাচক্র থেকে মূলাধার অবধি স্নায়ুপথে জোয়ারের জলের মতো উচ্ছ্বসিত প্রবাহ পায়। এতে প্রেমানন্দে দেহ প্লাবিত হয়। এর নাম তারুণ্যামৃত ধারার মান।
৩. এর ফলে সাধক ইচ্ছাশক্তি দ্বারা দেহ-মন নিয়ন্ত্রণের অধিকার পায় এবং ইড়া পিঙ্গলা সুষুম্না নাড়িপথে শুক্র ইচ্ছামতো চালু রেখে অজরামরবৎ বোধগত সামরস্যজাত পরমানন্দ বা সহজানন্দ উপভোগ করতে থাকে। এরই নাম লাবণ্যমৃত পারাবারে স্নান। এতে স্কুল শৃঙ্গারের আনন্দই স্থায়ীভাব স্বরূপ শৃঙ্গারানন্দ বা সামরস্য লাভ করে। প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাস দ্বারা দেহরূপ দুগ্ধভাণ্ড শৃঙ্গার-রূপ মথনদণ্ড সাহায্যে প্রবহমান নবনীতে পরিণত করা যায়। এর ফলে জরা-গ্লানি দূর হয় এবং সজীবতা ও প্রফুল্লতা সদা বিরাজমান থাকে।
বাঙলা ও বাঙালি
মা জন্ম দেয়, মাটি লালন করে।
তাই দেশের মাটিকে মায়ের মতোই ভালবাসতে হয়। এক সময় মায়ের প্রয়োজন ফুরায়। কিন্তু মাটির প্রয়োজন মৃত্যুর পরেও থেকে যায়। মানুষের জীবন একাকিত্বে সম্ভব নয়, তাই পরিজন-প্রতিবেশী নিয়েই যাপন করতে হয় তার জীবন। এদের সঙ্গে দ্বন্দ্বে ও মিলনে, সহযোগিতায় ও বিরোধেই তার জীবনের বিকাশ ও বিস্তার সম্ভব। অতএব চেতনার গভীরে দেশের মাটি ও মানুষের গুরুত্ব উপলব্ধি করাই স্বাজাত্য ও স্বাদেশিকতা।
দেশের মাটি ও মানুষের অন্তরঙ্গ পরিচয় জানা থাকলেই স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করা সম্ভব এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাও হয় সহজ। কেননা জিজ্ঞাসার মাধ্যমেই কেবল স্বদেশের মাটির জল ও বায়ু, দোষ ও গুণ এবং স্বদেশী মানুষের মন ও মেজাজ, যন্ত্রণা ও আনন্দ, সমস্যা ও সম্পদ, ভয় ও ভরসার কথা জানা যায়।
আলোচ্য গ্রন্থে [এই প্রবন্ধ অজয় রায়ের বাঙালা ও বাঙালি গ্রন্থের ভূমিকা স্বরূপ লিখিত।] লেখক বাঙালির কাছে বাঙলা ও বাঙালির অতীত পরিচয় তুলে ধরবার মহৎ প্রয়াসে নিরত। এ গ্রন্থ পণ্ডিতদের জন্যে নয়, লেখাপড়া-জানা আত্ম-জিজ্ঞাসু বাঙালির জন্যে। এই দেশের ও মানুষের উদ্ভব ও বিকাশ, ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য, গৌরব ও লজ্জা, শক্তি ও দুর্বলতা, সম্পদ ও সমস্যা, আনন্দ ও যন্ত্রণা-দোষ ও গুণ, ভয় ও ভরসা, প্রীতি ও ঘৃণা, দ্বন্দ্ব ও মিলন, আশা ও নৈরাশ্য, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মগ্লানি, আত্মসম্মানবোধ ও আত্মরতি, আদর্শবাদ ও নীতিহীনতা, সুকৃতি ও দুষ্কৃতি, সংগ্রাম ও পরবশ্যতা প্রভৃতির ইতিকথাই স্বদেশ ও স্বজাতির অন্তরঙ্গ পরিচয়ের তথা স্বরূপের অভিজ্ঞান।
বাঙলার রাঢ়-বরেন্দ্রই প্রাচীন। পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গ অর্বাচীন। রাঢ় ছিল অনুন্নত ও অজ্ঞাত। তাই বরেন্দ্র নিয়েই বাঙলার ইতিহাসের শুরু। মানুষের আদি নিবাস ছিল সাইবেরিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল। সেখান থেকেই নানা পথ ঘুরে আসে ভূমধ্যসাগরীয় দ্রাবিড়-নিগ্রো, সাইবেরীয় নর্ডিক মোঙ্গল। এরাই অস্টক, দ্রাবিড়, শামীয়, নিগ্রো, আর্য, তাতার, শক, হুন, কুশান, গ্রীক, মোঙ্গল, ভোটচীনা প্রভৃতি নামে পরিচিত। আমাদের গায়ে আর্য-রক্ত সামান্য, নিগ্রো-রক্ত কম নয়, তবে বেশি আছে দ্রাবিড় ও মোঙ্গল রক্ত, অর্থাৎ আমাদেরই নিকট-জ্ঞাতি হচ্ছে কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল, নাগা, কুকী, তিব্বতী, কাছাড়ী, অহোম প্রভৃতি।
এদেশে যারা বাস করত তারা ছিল আধা বর্বর। এদের নিকট-জ্ঞাতি নেপালী-বিহারীরা বৈদিক আর্যদের সংস্পর্শে এসে তাদের ভাষা-ধর্ম-সংস্কৃতি ও সমাজ বরণ করে। কিন্তু পীড়ন-শোষণ অসহ্য হওয়ায় যাদের দোহাই কেড়ে নির্যাতন চালানো হত, সেই দেব-দ্বিজ-বেদদ্রোহী হয়ে উঠে তারা। যুগে যুগে নেতৃত্ব দেন আজীবক, তীর্থঙ্কর ও বোধিসত্ত্ব নামে আখ্যাত বহু নেতা। অবশেষে দেব-দ্বিজ ও বেদ্রোহী গৌতম বুদ্ধ ও বর্ধমান মহাবীরের নেতৃত্বে পীড়নমুক্ত হল তারা।
এই জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমেই বাঙালিরা উত্তর ভারতীয় আর্য-ভাষা, লিপি, সংস্কৃতি, সমাজ ও নীতি বরণ করে সভ্য হয়ে উঠে। তাই কিছু প্রাচীন শব্দ, কিছু বাক্-রীতি, কিছু আচার সংস্কার ছাড়া বাঙালির বহিরাঙ্গিক অন্য স্বাতন্ত্র দুর্লক্ষ্য।
এভাবে যুগে যুগে বাঙালির ধর্ম, সমাজনীতি, পোশাক, প্রশাসনিক বিধি প্রভৃতি আচারিক ও আদর্শিক জীবনের প্রায় সবকিছুই এসেছে বিদেশী, বিজাতি ও বিভাষী থেকে।
তবু বাঙালির চিন্তার স্বকীয়তা, মানস স্বাতন্ত্র্য ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কখনো অবলুপ্ত হয়নি এবং তা একাধারে লজ্জার ও গৌরবের।
বাঙালি চিরকাল বিদেশী ও বিজাতি শাসিত। সাত শতকের শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত এবং পনেরো শতকের যদু-জালালুদ্দিন ছাড়া বাঙলার কোনো শাসকই বাঙালি ছিলেন না। এটি নিশ্চিতই লজ্জার এবং বাঙালি চরিত্রে নিহিত রয়েছে এর গূঢ় কারণ।
যে ভোগেচ্ছু অথচ কর্মকুণ্ঠ, তার জীবিকার্জনের দুটো পথ–ভিক্ষা ও চৌর্য। বাঙালির এই কাঙালপনার পরিচয় রয়েছে তার স্বসৃষ্ট উপদেবতা-অপদেবতা কল্পনায় ও তুকতাক, যাদু-টোনা, মন্ত্র-তন্ত্র-কবচ-মাদুলীপ্রীতিতে। আপাতসুখ ও আত্মরতি তাকে করেছে স্বার্থপর, ধূর্ত ও লোভী। তাই সে যৌথকর্মে অসমর্থ। তার বুদ্ধি ধূর্ততায়, তার সংকল্প উচ্ছ্বাসে, তার প্রয়াস স্বার্থে অবসিত। কালো পিঁপড়ের মতো সে নিঃসঙ্গ সুযোগসন্ধানী। এসব নিশ্চিতই বাঙালির স্থায়ী কলঙ্কের কথা।
কিন্তু তার গৌরব-গর্বের বিষয়ও কম নেই। সে তর্ক করে, যুক্তি মানে কিন্তু হৃদয়-বেদ্য না হলে জীবনে আচরণ করে না। তাই সে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও ইসলামধর্ম মুখে যতটা গ্রহণ করেছে, অন্তরে ততটা মানেনি। সে তার জীবন ও জীবিকার অনুকূল করে রূপান্তরিত করেছে ধর্মকে। সে পুজো করেছে তার স্বসৃষ্ট উপ ও অপ-দেবতার। সৃষ্টি করেছে স্বকীয় মতবাদ ও আচার-আচরণ বিধি। বৌদ্ধ যুগে বাঙালির কালচক্রযান, বজ্রযান, মন্ত্রযান, সহজযান; ব্রাহ্মণ্য সমাজে বাঙালির লৌকিক দেবতা-নিষ্ঠা, নব্যন্যায়, নব্যস্মৃতি, চৈতন্যের প্রেমবাদ; মুসলিম সমাজে সত্যপীরবাদ, যৌগিক-সূফী তত্ত্ব, ওহাবী-ফরায়েজী মতবাদ এবং রামমোহনের ব্রাহ্মমত তার সাক্ষ্য।
এভাবে দেশজ লৌকিক ধর্মই কালে কালে বাঙালির জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছে। বাঙালির স্বাধীনতাপ্রীতি, স্বাজাত্যবোধ ও সঙ্-শক্তির সাক্ষ্য নগণ্য বটে, কিন্তু তার মাটি ও মর্ত্যপ্রীতি সর্বত্র সুপ্রকট। আদিতে তারও ছিল কৌম জীবন। বাহ্যত কর্মবিভাগ সে স্বীকার করেছে,সমাজে কর্মগত সহযোগিতা ও সংহতির গুরুত্বও কখনো অস্বীকৃত হয়নি। কিন্তু তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র-প্রবণতা ও আত্মরতি ছাপিয়ে উঠেছিল তার সহমর্মিতা ও সমধর্মিতার বন্ধনকে।
যখন সে জৈন-বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে তখনো কৌমচেতনা ছিল প্রবল এবং সম্ভবত বৌদ্ধ-মৌর্য শাসনেও তার বিচলন ঘটেনি। ব্রাহ্মণ্যগুপ্ত শাসনেই বৃত্তিগত বিভাগ বর্ণবিভাগে বিকৃত হয়। কেননা সে-সময়ে ব্রাহ্মণ্যবাদীর সংখ্যা বাড়ে এবং বৌদ্ধ পাল আমলের প্রথম যুগে এ চেতনা ম্লান হলেও শেষের দিকে শঙ্করাচার্যের নব ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবে এবং উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণাদি কর্মচারীর বাহুল্যে ক্ষয়িষ্ণু বৌদ্ধ সমাজ দ্রুত অপসৃত হয়ে বর্ণে বিন্যস্ত ব্রাহ্মণ্য সমাজ গড়ে উঠতে থাকে আর ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন আমলে তা পূর্ণতা লাভ করে। এজন্যেই বাঙালির বর্ণবিন্যাস নিতান্ত কৃত্রিম। মোটামুটি ভাবে দশ থেকে ষোলো শতক অবধি মেল ও পটি বন্ধনের কাজ চলে। বল্লাল চরিত, দৈবকী-ধ্রুবানন্দ-পঞ্চানন ঘটক ও জাতিমালা কাছারি তার সাক্ষ্য। এমনি করে নিবর্ণ বৌদ্ধ সমাজ থকে বর্ণাশ্রিত হিন্দু সমাজ গড়ে উঠে। ফলে এখানকার হিন্দু-মুসলমান–কারো জাত-বর্ণ পরিচয় সন্দেহাতীতরূপে যথার্থ নয়। বিশেষ করে দ্রাবিড়-নিগ্রো-মোঙ্গল কারো মধ্যেই যখন বর্ণবিভাগ ছিল না, তখন এ যে আরোপিত ও অর্বাচীন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।
প্রাচীনকালে এখানে লোকসংখ্যা ছিল কম, গোত্রে বিভক্ত কৌমের নিবাস ছিল অঞ্চলে সীমিত। কাজেই জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য ধর্মে দীক্ষার পরেই তারা গৌত্রিক গ্রাম থেকে ধর্মীয় সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। কিন্তু স্বাদেশিকতা নিতান্ত আধুনিক চেতনা। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ভাষিক ঐক্যের ফলে তারা স্থানিক ঐক্য লাভ করেছিল বটে; কিন্তু দেশগত জীবন-চেতনা ছিল অনুপস্থিত। তাই বাঙালি হিন্দু ছিল উত্তর ভারতীয় আর্য-গৌরবে এবং রাজপুত-মারাঠার ঐতিহ্যগর্বে স্ফীত। আর মুসলমান– ছিল আরব-ইরানীর জ্ঞাতিত্ব মোহে ও গৌরবে অভিভূত। ইদানীং-পূর্ব যুগে কেউ সুস্থ ও স্বস্থ ছিল না। স্বদেশে প্রবাসী এই বাঙালির রাজনৈতিক দুর্ভাগ্য এবং সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র চেতনার ও স্বাদেশিক কর্তব্যবুদ্ধির বিরলতার কারণ এই।
আজ ভেবে দেখবার সময় এসেছে : মৌর্য-গুপ্ত-পাল-সেন-তুর্কী-মুঘল আমলে বাঙালি কী স্বাধীন ছিল– সুখী ছিল? স্বাধীন পাল কিংবা সুলতানী আমল কী বাঙালির স্বাধীনতার যুগ? বারোভূইয়ার বিদ্রোহ ও বীরত্ব কী স্বাধীনতাকামী বাঙালিরও সংগ্রাম ও ত্যাগের ঐতিহ্য? জাতীয়তার ভিত্তি হবে কী-গোত্র, ধর্ম, বর্ণ, দেশ কিংবা রাষ্ট্র?
বাংলাদেশ ক্বচিৎ একচ্ছত্র শাসনে ছিল। তাই বাঙলা দেশান্তর্গত সব ঐতিহ্যে সর্ব বাঙালির অধিকার ছিল না। আঞ্চলিক মন, মনন ও সংস্কৃতির স্পষ্ট ছাপ আজো জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিদ্যমান। সাহিত্য ক্ষেত্রে এ আঞ্চলিকতা বিস্ময়করভাবে সুপ্রকট। যেমন ধর্মমঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল হয়েছে রাঢ় অঞ্চলে, মনসামঙ্গল হয়েছে পূর্ববঙ্গে, বৈষ্ণব সাহিত্য হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে; বাউল প্রভাব পড়েছে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে। সত্য-পীর বা সত্যনারায়ণ-কেন্দ্রী উপদেবতার প্রভাব-প্রসার ক্ষেত্র হচ্ছে দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গ। গীতিকা হয়েছে ময়মনসিংহে-চট্টগ্রামে, মুসলিম রচিত সাহিত্যের বিশেষ বিকাশ ঘটেছে চট্টগ্রামে। গাঁজান, গম্ভীরা, বৈষ্ণবগীতি, বাউলগান, ভাবাইয়া, ভাটিয়ালী প্রভৃতিরও স্থানিক বিকাশ লক্ষণীয়।
দারু, কারু ও চারু শিল্পের ক্ষেত্রেও আঞ্চলিকতা গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকাই মসলিন ও শঙ্খশিল্প, সিলেটী গজদন্ত ও বেতশিল্প, নদীয়ার পাট-শিল্প, রাজশাহী-মালদাহ-মুর্শিদাবাদের রেশমশিল্প, পাবনা-টাঙ্গাইলের বস্ত্রশিল্প, চট্টগ্রামের নৌ ও দারু-শিল্প স্মতব্য।
বাঙালির লজ্জা ও গৌরবের কিছু ইঙ্গিত দিলাম। কিন্তু বাঙালি যেখানে স্বকীয় মহিমায় সমুন্নত, যেখানে সে অতুল্য এবং প্রাচ্যদেশে প্রায় অজেয়, তা বিদ্যা ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে বাঙালির অবদান। তার সাহিত্য ও তার দর্শন তার গৌরবের ও গর্বের এবং অপরের ঈর্ষার বস্তু।
আলোচ্য গ্রন্থে লেখক বাঙালির সুচির কালের সামগ্রিক পরিচয় তুলে ধরতে চেয়েছেন এবং তাঁর প্রয়াস অনেকাংশে সফল ও সার্থক হয়েছে বলেই মনে করি। আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত আজো প্রায় অনুঘাটিতই রয়ে গেছে। কাজেই প্রমাণে-অনুমানে রচিত হয়েছে আমাদের ইতিহাসের ভিত। এই গ্রন্থের লেখক অদ্যাবধি আবিষ্কৃত ও অনুমিত তথ্য ও তত্ত্বের স্বাধীন প্রয়োগে রচনা করেছেন এ গ্রন্থ। এ গ্রন্থের মাধ্যমে উৎসুক ও জিজ্ঞাসু বাঙালির আত্মদর্শন হবে। এটি গ্রন্থকারেরও সম্ভবত লক্ষ্য। এ গ্রন্থের অনেক গুণ–ভাষা স্বচ্ছ ও সচল, ভঙ্গি প্রাঞ্জল, বক্তব্য সুস্পষ্ট। কিন্তু স্থানে স্থানে অসতর্কতার ছাপ রয়েছে, তথ্যের ভুলও কিছু আছে। সামান্যীকৃত (generalised) সিদ্ধান্তপ্রবণতা কম হলেই ভালো হত।
ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন, ডক্টর তমোনাশ দাসগুপ্ত, ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, ডক্টর সুকুমার সেন, ডক্টর আবদুর রহিম, ডক্টর মোমতাজুর রহমান তরফদার প্রমুখ রচিত সমাজ-সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থগুলো বাঙলা ও বাঙালির কালিক ইতিহাস। আর শ্রীঅজয় রায়ের বইটি সাধারণের জন্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। উপরোক্ত গ্রন্থগুলো পাঠে এই গ্রন্থে লব্ধ জ্ঞান পূর্ণতা পাবে। সুচির বাঙালির জগৎ ও জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত এমনি আলোচনা গ্রন্থ আরো আরো কামনা করি। এমনি আত্ম পরিচিতিমূলক গ্রন্থে বাঙালির আজ বড় প্রয়োজন।
এক্ষেত্রে পথিকৃৎ শ্রীঅজয় রায়কে কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানিয়ে এখানেই বক্তব্যের শেষ করছি।
বাঙলায় সূফী প্রভাব
০১.
মুসলিম বিজয়ের পূর্বে বাঙলাদেশে সূফী-দরবেশ এসেছিলেন কী না, ইতিহাস তা বলতে পারে না। তবু পাহাড়পুরে ও ময়নামতীতে আব্বাসীয় খলীফাদের মুদ্ৰাপ্রাপ্তি ও সোলেমান, খুরদাদবেহ, আলইদ্রিসী, আলমাসুদী প্রমুখ লেখকদের এবং দুদুল আলম গ্রন্থের বিবরণের প্রমাণে স্বীকার করতে হয় যে, অন্তত আটশতক থেকে আরবদের সঙ্গে বাঙলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক শুরু হয়। অবশ্য Periplus in the Erythrean Sea-র আলোকে যাচাই করলে এ সম্পর্ক খ্রীস্টীয় প্রথম শতক অবধি পিছিয়ে দেয়া সম্ভব।
চট্টগ্রাম বন্দরে আরব বেনেরা বছরের কয়েক মাস থেকে যেত। সে-সূত্রে বন্দর এলাকায় তারা বৈবাহিক সম্পর্ক পাতিয়েছিল কি-না জানা নেই। তবে পরবর্তীকালের পর্তুগীজ প্রভৃতি য়ুরোপীয় বেনেদের জীবনযাপন রীতির কথা স্মরণ রাখলে, এ সম্পর্কও অনুমান করা চলে। ইংরেজ আমলে দেখেছি, বাঙালি মুসলমানেরা বার্মায় বর্মী স্ত্রী গ্রহণ করত আর তাদের সন্তানেরা জোরবাদী নামে পরিচিত হত। এমনি সঙ্কর মুসলমান হয়তো কিছুটা ছিল চট্টগ্রাম বন্দর এলাকায়। মুসলমান ব্যবসায়ীদের পাহাড়পুরে, ময়নামতীতে, কিংবা কামরূপে যাতায়াতও ছিল কি-না বলা যাবে না। কেননা, তাদের মুদ্রা ওসব অঞ্চলে অন্যভাবেও নীত হওয়া সম্ভব। কিন্তু ইসলামের প্রচার ও প্রসার যুগে মুসলিম বেনে বা তাদের সঙ্গী কেউ ইসলামপ্রচারে আগ্রহী হয়নি এমন কথা ভাবব কেন? আমাদের মনে হয়, তখনো মুসলিম সমাজে সূফীমতবাদ প্রসার লাভ করেনি বলে এবং দণ্ডশক্তি বিধর্মীর হাতে ছিল বলে এদেশে যারা ইসলাম প্রচার করতে এসেছিলেন বা অন্যসূত্রে এসে ইসলাম প্রচারের চেষ্টায় ছিলেন, তারা বিশেষ শ্রদ্ধা কিংবা সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। দরবেশ না হলে তথা কেরামতির আভাস না পেলে অজ্ঞলোকেরা ভক্তি করবার কারণ খুঁজে পায় না। কাজেই তেমন লোকের স্মৃতি রক্ষার গরজও বোধ করে না। আর যদি মুসলিম বিজয়ের পূর্বে জালালউদ্দীন তাবরেজীর (?) মতো সূফীরা এসেও থাকেন তাহলেও মুসলিম-বিরল কিংবা বিহীন বিধর্মীর রাজ্যে তার স্মৃতিরক্ষার আয়োজন করবার লোকই ছিল না।
সূফীমত প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে সূফীরা বিজিত ভারতেও আসতে শুরু করেন। তখন থেকেই খানকা ও দরগাকেন্দ্রী ইতিহাসেরও আরম্ভ।
কিন্তু চৌদ্দ শতকের এক সূফীর সাক্ষ্যে প্রমাণিত বাঙলাদেশে তার আগেই বহু সূফীর আগমন ঘটেছে। তারা বিভিন্ন মত-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শেখ আলাউল হক পাণ্ডুবীর সাগরেদ সৈয়দ আশরাফ জাহাঙ্গীর সিমনানী কর্তৃক জৌনপুর সুলতান ইব্রাহীম শর্কীর নিকট লিখিত পত্রে আছে :
God be praised! What a good land is that Bengal where numerous saints and asceties came from many directions and made it their habitation and home. For example at Devgaon, followers of Hazrat Shaikh Shahabuddin Suhrwardi are taking their eternal rest. Several saints of the Suhrwardi order are lying burried in Mahisun and this is the case with saints of Jalalia order in Deotala. In Narkoti some of the best companions of the Shaikh Ahmed Damishqi are found. Hazrat Shaikh Sharfuddin Tawwama, one of the twelve of the Qadar Khani order whose chief pupil was Hazrat Shaikh Sharfuddin Maneri is lying burried at Sonargaon. And then there was Hazrat Badr Alam and Badr Alam Zahidi. In short, in the country of Bengal what to speak of the cities there is no town and no village where holy saints did not come and settle down. Many of the saints of the Suhrwardi order are dead and gone under earth but those still alive are also in fairly large number.
এতে বোঝা যায়, যে চৌদ্দ শতকের মধ্যেই বাঙলা দেশে সূফীপ্রভাব গভীরতা ও বিস্তৃতি লাভ করে।
কিন্তু যে কয়জন প্রাচীন সূফীর কাহিনী এবং খানকা ও দরগাহর খবর আমরা জানি, তাঁদের আগমন ও অবস্থিতি কাল সম্বন্ধে বিদ্বানেরা একমত নন। যেমন বাবা আদম শহীদ। বিক্রমপুরস্থিত রামপালের এই আদম শহীদ বিক্রমপুরের এক সেন রাজা বল্লালের সমসাময়িক। অনন্দভট্ট রচিত বল্লাল চরিতম সম্ভবত এঁরই জীবন চরিত লক্ষণসেনের পিতা প্রখ্যাত বল্লালসেনের নয়। বল্লাল চরিতোক্ত বায়াদুমবা সম্ভবত বাবা আদমেরই নামবিকৃতি। নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে বল্লাল সেন চৌদ্দ শতকের শেষার্ধের লোক। কাজেই বাবা আদমও ঐ সময়ের।
চট্টগ্রামের পীর বদরুদ্দীন বদর-ই-আলম, বর্ধমানের কালনার বদর সাহিব, দিনাজপুরের হেমতাবাদের বদরুদ্দীন এবং বদর-মোকান খ্যাত বদর শাহ্ বা বদর আউলিয়া আর মাঝিমাল্লার পাঁচপীরের অন্যতম পীর বদর সম্ভবত অভিন্ন ব্যক্তি। চট্টগ্রামে এর অবস্থিতিকাল কারো মতে ১৩৪০ আর কারো ধারণায় ১৪৪০ খ্রীস্টাব্দ।
শেখ জালালউদ্দীন তাবরেজীর নাম শেকশুভোদয়ার সঙ্গে জড়িত। কেউ কেউ একে জাল গ্রন্থ বলে বিবেচনা করেন। এই গ্রন্থের লেখক হলায়ুধ মিশ্র রাজা লক্ষ্মণ সেনের সচিব ছিলেন। তিনি যদি ১২১০-১২ খ্রীস্টাব্দের পর বেঁচে থাকেন, তাহলে শেখ শুভোদয়া তাঁর রচনা হওয়া সম্ভব। তবে স্বীকার করতে হবে যে ভাষার বিকৃতি ও প্রক্ষিপ্ত তথ্যে গ্রন্থটি বিদ্বানদের বিভ্রান্তির কারণ হয়েছে। ইতিহাস-বিরল সে-যুগে গ্রন্থকার হিসেবে হলায়ুধ মিশ্রের ও শাসকরূপে লক্ষ্মণ সেনের নাম জড়িয়ে, আর্যা প্রভৃতির প্রাচীনরূপ রক্ষা করে মোলো-সতেরো শতকে জালগ্রন্থ রচিত হয়েছে, অনুমান করতে অনেকখানি কল্পনার প্রয়োজন। শেখ শুভোদয়া সূত্রে কারো কারো বিশ্বাস, শেখ জালালউদ্দীন তাবরেজী লক্ষ্মণ সেনের আমলে লখনোতিতে তথা বাঙলায় বাস করতেন। অমৃতকুণ্ড তাঁরই আগ্রহে অনূদিত হয়। তাঁরাই মাহাত্ম্য-মুগ্ধ হলায়ুধ মিশ্র তাঁর কৃতিকথা বর্ণনা করেছেন শেখ শুভোদয়ায় (শেখের শুভ উদয়)। আবদুর রহমান চিশতির মতে জালালউদ্দীন তাবরেজীর পুরো নাম ছিল আবুল কাশেম মখদুম শেখ জালাল তাবরেজী। তিনি শেখ শিহাবুদ্দীন সোহরওয়ার্দীর সাগরেদ ছিলেন। তিনি কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী, বাহাউদ্দীন জাকারিয়া, নিযামুদ্দীন মুগরা ও দিল্লীর সুলতান শামসুদ্দীন ইলতুৎমিসের (১২১০-৩৬) সমসাময়িক। জন্মস্থান তাব্রিজ থেকে দিল্লী এলে তাকে সুলতান ইলতুৎমিস অভ্যর্থনা করেন। এ তথ্যে আস্থা রাখলে স্বীকার করতে হবে জালালউদ্দীন তাবরেজী লক্ষ্মণ সেনের আমলে বাংলায় আসেননি। কেউ কেউ আবার শেখ জালালউদ্দীন তাবরেজী ও সিলেটের জালালউদ্দীন কুনিয়াঈকে অভিন্ন মনে করেন। শেখ জালালউদ্দীন বহুল আলোচিত সূফী।১৫ ময়মনসিংহ জেলার মদনপুরে শাহ সুলতান রুমী নামে এক সূফীর দরগাহ্ আছে। ইনি ৪৪৫ হিজরি বা ১০৫৩-৫৪ সনে ওখানে বিদ্যমান ছিলেন বলে পরবর্তীকালে দলিলসূত্রে দাবী করা হয়। এক কোচ রাজা তার হাতে ইসলামে দীক্ষিত হয়ে তাকে মদনপুর গ্রাম দান করেন বলে ময়মনসিংহ Gazetter-এ উল্লেখ আছে। কিন্তু আরো প্রায় সাড়ে তিনশ বছর পরে উক্ত জেলায় কোচ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অতএব, উক্ত কোচ রাজা কোনো কোচ জমিদার হবেন, কিংবা সুলতান রুমী চৌদ্দ শতকের লোক।
পাবনা জেলার শাহজাদপুরে রয়েছে মুখদুম শাহ্ দৌলা শহীদের দরগাহ্। ইনি জালালউদ্দীন বোখারীর সমসাময়িক ছিলেন। অতএব ইনি বারো-তেরো শতকের লোক।
বর্ধমানের মঙ্গলকোট গায়ে মখদুম শাহ মাহমুদ গজনবী ওর্ষে শাহরাহী পীরের দরগাহ রয়েছে। ইনি স্থানীয় রাজা বিক্রম কেশরীর সাথে লড়েছিলেন বলে কিংবদন্তি আছে।
বগুড়ার মহাস্থানগড়ের শাহ্ সুলতান মাহি-আসোয়ারের স্বীকৃতি আওরঙজীবের সনদসূত্রেও (১০৯৬ হি. ১৬৮৫-৮৬) মিলে। তার সম্বন্ধে লোকশ্রুতি এই যে তিনি মুসলিম-বিদ্বেষী রাজা বলরাম ও পরশুরামকে হত্যা করেন। পরশুরামের ভগ্নী শিলাদেবী করতোয়া নদীর যেখানে ডুবে মরেছিল, তা এখনো শিলাদেবীর ঘাট নামে পরিচিত। ইনি সম্ভবত চৌদ্দশতকের লোক। মনে হয় মাহি-আসোয়ার (মৎস্যাকৃতি নৌকার আরোহী) খ্যাতির লোকেরা চৌদ্দশতকের পরের লোক নন। কেননা পনেরো শতকে আরব-ভারতের স্থলপথ জনপ্রিয় হয়। আর ষোলো শতকে পর্তুগীজেরা জলপথ নিয়ন্ত্রণ করত।
সিলেটের শাহ্ জালাউদ্দীন কুনিয়াঈ চৌদ্দশতকের দ্বিতীয় পাদে বাঙলাদেশে আসেন। ইবন বতুতা (১৩৩৮ সনে) সিলেটে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইনি রাজা গৌরগোবিন্দকে পরাজিত করে সিলেট অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন।
মখদুম-উল-মুলক শেখ শরফুদ্দীন ইয়াহীয়া ও তাঁর উস্তাদ শরফুদ্দীন আবু তাওয়ামাহ সোনারগাঁয়ে (১২১০-৩৬, বা ১২৭০-৭১, কিংবা ১২৮২-৮৭ খ্রীস্টাব্দে) এসেছিলেন। ইনি এবং মকুল হোসেনে মুহম্মদ খান-বর্ণিত শেখ শরফুদ্দীন অভিন্ন ব্যক্তি কী না বলবার উপায় নেই।
শেখ বদিউদ্দীন শাহ মাদার সিরিয়া থেকে এসেছিলেন। এঁর পিতার নাম আবু ইসহাক শামী। ইনি মুসা নবীর ভাই হারুনের বংশধর। ইনিই সম্ভবত শূন্য পুরাণোক্ত নিরঞ্জনের রুম্মার দম মাদার। এবং মাদারীপুরও সম্ভবত তাঁর নাম বহন করছে। চট্টগ্রামের মাদারবাড়ী, মাদার শাহ্ এবং দরগাহ সংলগ্ন পুকুরের মাছের মাদারী নাম, শাহ্ মাদারের স্মরণার্থ বাঁশ তোলার বার্ষিক উৎসব প্রভৃতি মাদারিয়া সম্প্রদায়ের সূফীর বহুল প্রভাবের পরিচায়ক বলে ডক্টর এনামুল হক মনে করেন।
মখদুম জাহানিয়া জাহানগত ওফে জালালউদ্দীন সুপুশ (Surkpush) নামে এক দরবেশ বাঙলায় এসেছিলেন। জাহানসতের মৃত্যু হয় ১৩৮৩ খ্রীস্টাব্দে এবং উছে (Uchh) তার সমাধি আছে।
শেখ আখি সিরাজউদ্দীন উসমান নিযামুদ্দীন আউলিয়ার খলিফা ছিলেন। ইনি পাণ্ডুয়ার শেখ আলাউল হকের পীর। ইনি চৌদ্দ-পনেরো শতকের দরবেশ। তাঁর প্রভাবেই মুখ্যত বাঙলাদেশে চিশতিয়া তরিকার প্রসার হয়। পীরের নামানুসারে বিভিন্ন চিশতিয়া পীরের শিষ্যরা বিভিন্ন নামে পরিচিত হতেন। আলাউল হকের শিষ্যরা আলাহ, তাঁর পুত্র নূর কুতুব-ই-আলমের সাগরেদরা নূরী২৮ এবং আলাউলের খলিফা শেখ হোসেন ধুক্কারপোশ (Dhukkarposh)-এর সম্প্রদায়ের সূফীরা হোসেনী নামে পরিচিত ছিল। শেখ আলাউল হক ইসলামের উন্মেষযুগের মুসলিম সেনাপতি খালিদ-বিন-ওলীদের বংশধর। সেজন্যে তাঁর শিষ্যরা খালিদিয়া নামেও অভিহিত হতেন। আলাউল হকেরই পুত্র ছিলেন নূর কুতুব-ই-আলম। গণেশ-যদুর আমলে গৌড়ের রাজনীতিতে আলাউল হকের পরিবার স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। নূর কুতুব-ই-আলমের পুত্র শেখ আনোয়ার রাজা গণেশ কর্তৃক সোনারগাঁয়ে নির্বাসিত ও পরে নিহত হন। নূর কুতুব-ই আলমের ভ্রাতুস্পুত্র শেখ জাহিদও সোনারগাঁয়ে নির্বাসিত হয়েছিলেন। জালালুদ্দীন মোহাম্মদ শাহ ওফেঁ যদু শেখ জাহিদের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন।
মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাগীর সিমনানী শেখ আলাউল হকের শিষ্য ছিলেন। এঁর চিঠিগুলো সেকালের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের মূল্যবান উপকরণ ও নির্ভরযোগ্য দলিল। সৈয়দ আশরাফ সিমনানী জৌনপুর সুলতান ইব্রাহীম সৰ্কীর সমসাময়িক ছিলেন। সিমনানী ইব্রাহীম সকীকে লিখিত এক পত্রে বদর আলম ও বদর আলম জাহিদী নামে দুইজন সূফীর উল্লেখ করেছেন। শেখ হোসেন ধুক্কারপোশ (Dhukkarposh)-এর ছেলে রাজা গণেশ কর্তৃক নিহত হলে সিমনানী তাঁকে প্রবোধ দিয়ে যে পত্র লেখেন, তা থেকে আভাস মিলে যে, গণেশ কিছু সোহরাওয়ার্দীয়া ও রুহানিয়া সূফীকে হত্যা করেন। Those who Traverse the path of God, have many calamities to suffer from. It is hoped through the spiritual grace of the souls of Suhrawardia and Ruhania saints of the part, of that in near future that kingdom of Islam will be free from the hands of the luckless nonbelievers.us
শেখ বদরুল ইসলাম নূর কুতুব-ই-আলমের সমসাময়িক। রিয়াজুস-সালতিন৩২-এ বর্ণিত ঘটনায় প্রকাশ : রাজা গণেশের দরবারে ইনি রাজাকে অভিবাদন না করেই আসন গ্রহণ করেন। রুষ্ট রাজা তাঁকে হত্যা করে তার ঔদ্ধত্যের শাস্তি দেন।
এঁরা ছাড়া শাহ্ সফিউদ্দীন, জাফর খান গাজী৩৩ খাঁ জাহান আলী, শাহু আনোয়ার কুলি হালবী, ইসমাইল গাজী, মোল্লা আ, শাহ জালাল দাখিনী (মৃত্যু ১৪৭৬ খ্র.), শাহ মোয়াজ্জম দানেশমন্দ ওর্কে মৌলানা শাহ্ দৌলা (রাজশাহী : বাঘা), শাহ আলী বাগদাদী (মীরপুর, ঢাকা), শেখ ফরিদউদ্দীন শাহ্, লঙ্গর শাহ নিয়ামতুল্লাহ, শাহ লঙ্কাপতি প্রভৃতি দরবেশের নাম উল্লেখ্য।
জালালুদ্দীন তাবরেজী (মৃত্যু ১২২৫ খ্রী.), মখদুম জাহানিয়া (১৩০৭-৮৩) ও শাহজালাল কুনিয়াঈ (মৃত্যু ১৩৪৬) সোহরাওয়ার্দীয়া মতবাদী ছিলেন।
শেখ ফরিদউদ্দিন শখরগঞ্জ (১১৭৬-১২৬৯), আখি সিরাজুদ্দীন (মৃ. ১৩৫৭), আলাউল হক (মৃ. ১৩৯৮), শেখ নাসিরুদ্দীন মানিকপুরী, মীর সৈয়দ আশরাফ জাহাগীর সিমনানী, শেখ নুর কুতুব-ই-আলম (মৃ. ১৪১৬), শেখ জাহিদ প্রমুখ চিশতিয়া সম্প্রদায়ের সূফী ছিলেন।
শাহ সফীউদ্দিন (মৃত্যু ১২৯০-৯৫?) কলন্দরিয়া সূফী ছিলেন।
শাহ্ আল্লাহ্ মদারিয়া এবং শেখ হামিদ দানিশমন্দ নকশবন্দিয়া সূফী ছিলেন।৪০ ষোলো শতক অবধি চট্টগ্রামের সূফী শাহ্ সুলতান বল্খী (বায়জিদ?), শেখ ফরিদ, পীর বদর আলাম, কাতাল পীর, শাহ মসন্দর বা মোহসেন আউলিয়া, শাহপীর, শাহাদ প্রমুখ এবং কবি মুহম্মদ খানের মাতৃকূলের পীর শরফউদ্দীন থেকে সদরজাহা আবদুল ওহাব ওর্ষে শাহ ভিখারী অবধি অনেক পীর প্রখ্যাত।
গৌড়ের সুলতানদের মধ্যে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ্, সিকান্দর শাহ্, গিয়াসুদ্দীন আজম শাহ্, জলালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ্ (যদু), রুকনুদ্দীন বারবক শাহ্ প্রমুখের দরবেশ ভক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
আবার শাহ্ জালালউদ্দীন কুনিয়াঈ, আলাউল হক, নুর কুতুব-ই-আলম, আশরাফ জাহাগীর সিমনানী, ইসমাইল গাজী, জাফর আলী খা, খান জাহান খান প্রমুখ সূফীরা রাজনীতি ও সরকারি কর্মে নিযুক্ত ছিলেন।
আর্তের সেবা, কাঙাল ভোজন, রোগীর চিকিৎসা ও কেরামতি প্রভৃতি দ্বারাই সূফীরা গণমন জয় করেন।
.
০২.
মুসলমানদের বিশ্বাস : হযরত মুহম্মদ হজরত আলীকে তত্ত্ব বা গুপ্ত জ্ঞান দিয়ে যান। হাসান, হোসেন, খাজা কামীল বিন জয়ীদ ও হাসান বসরী সে-জ্ঞান আলী থেকে প্রাপ্ত হন। এই কিংবদন্তির কথা বাদ দিলে হাসান বসোরী (মৃ. ৭২৮ খ্র.), রাবিয়া (মৃ. ৭৫৩), ইব্রাহীম আদহম (মৃ. ৭৭৭), আবু হাশিম (মৃ. ৭৭৭), দাউদ তায়ী (মৃ ৭৮১), মারুফ করখী (মৃ ৮৫) প্রমুখই সূফী মতের আদি প্রবক্তা।
পরবর্তী সূফী জুননুন মিশরী (মৃ. ৮৬০), শিবলী খোরাসানী (মৃ. ৯৪৬), জুনাইদ বাগদাদী (মৃ. ৯১০) প্রমুখ সাধকরা সূফীমতকে লিপিবদ্ধ, সুশৃঙ্খলিত ও জনপ্রিয় করে তোলেন। আল্লাহ আকাশ ও মর্ত্যের আলো স্বরূপ। আমরা তার (মানুষেরা) ঘাড়ের শিরা থেকেও কাছে (রয়েছি)। –এই প্রকার ইঙ্গিত থেকেই সূফীমত বিশ্বব্রহ্ম বা সর্বেশ্বরবাদের তথা অদ্বৈতবাদের দিকে এগিয়ে যায়। জিকর বা জপ করার নির্দেশ মিলেছে কোরানের অপর এক আয়াতে অতএব (আল্লাহকে) স্মরণ কর। কেননা তুমি একজন স্মারক মাত্র।
সৃষ্টি ও স্রষ্টার অদৃশ্য লীলা ও অস্তিত্ব বুঝবার জন্যে বোধি তথা ইরফান কিংবা গুহ্যজ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। এ প্রয়োজনবোধ ও রহস্যচিন্তাই সূফীদের বিশ্বব্রহ্মবাদী বা সর্বেশ্বরবাদী করেছে। এই চিন্তা বা কল্পনার পরিণতিই হচ্ছে হমহউস্ত (সবই আল্লাহ্) বিশ্বব্রহ্মতত্ত্ব তথা সর্বং খন্বিদং ব্রহ্মতত্ত্ব। এই হল তৌহিদ-ই-ওজুদী তথা আল্লাহ্ সর্ব ভূতে বিরাজমান–এই অঙ্গীকারে আস্থা স্থাপন।
বায়জিদ, জুনাইদ বাগদাদী, আবুল হোসেন ইবনে মনসুর হল্লাজ এবং আবু সৈয়দ বিন আবুল খয়ের খোরাসানী (মৃত্যু ১০৪৯ খ্র.) প্রমুখ প্রথম যুগের অদ্বৈতবাদী সূফী। শরীয়তপন্থ বিরোধী এসব সূফীদের অনেককেই নতুন মত পোষণ ও প্রচারের জন্যে প্রাণ হারাতে হয়। মনসুর হল্লাজ, শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়ার্দী, ফজলুল্লাহ প্রমুখ এভাবেই শহীদ হন।
ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক বলেন–ভারতে সূফী প্রভাব পড়িবার পূর্ব হইতে, সূফীমতবাদ ভারতীয় চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট হইতে থাকে। খ্রীস্টীয় একাদশ শতাব্দীতেই ভারতে সূফীমত প্রবেশ করে। তৎপর্বের সূফীমতেও ভারতীয় দর্শন ও চিন্তাধারার স্পষ্ট চাপ দেখিতে পাই। তার মতে এ প্রভাব পড়ে ভারতীয় পুস্তকের আরবি-ফারসি অনুবাদের মাধ্যমে ও ভ্রাম্যমাণ বৌদ্ধভিক্ষুর সান্নিধ্যে। এবং আলবিরুনীর অনুবাদ, পাতঞ্জল যোগ এবং কপিল সাংখ্য তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয়ই এ প্রভাবের মুখ্য কারণ। বায়জিদ বোস্তামীর ভারতীয় (সিন্ধু দেশীয়) গুরু বুআলীর প্রভাবও এক্ষেত্রে স্মরণীয়। তিনি আরও বলেন, (বাঙলা) দেশে সূফীমত প্রচার ও বহুল বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সহজিয়া ও যোগ সাধন প্রভৃতি পন্থা, বঙ্গের সূফীমতকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে থাকে। কালক্রমে বাঙলার সূফী মতবাদের সহিত এদেশীয় সংস্কার, বিশ্বাস প্রভৃতিও সম্মিলিত হইতে থাকে। এবং সূফীমতবাদ ও সাধনপদ্ধতি ক্রমে ক্রমে যোগসাধন প্রভৃতি হিন্দুপদ্ধতির সঙ্গে একটা আপোষ করিয়া লইতে থাকে।
…… চিশতীয় ও সুহরদীয়হ সম্প্রদায়দ্বয়ের সাধনা, ভারতে আগমন করার পূর্ব হইতেই অনেকখানি ভারতীয় ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ভারতে আগমনের পর, এদেশীয় সাধনার সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ যোগসূত্রের সৃষ্টি হইল; ভারতের প্রাণের সহিত আরব ও পারস্যের প্রাণের ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটিয়া গেল। ভারতবিখ্যাত সাধক কবীর (১৩৯৮-১৪৪০ খ্র.) উক্ত প্রাণত্রয়ের পুণ্যতীর্থ প্রয়োগক্ষেত্রে পরিণত হইলেন। তাঁহার মধ্যে ভারতীয় যোগ সাধনা ও সূফীদের তস্ববফ বা ব্রহ্মবাদ সম্মিলিত হইল। সূফীরা সাক্ষাত্তাবে তাহার ভিতর দিয়া ভারতীয়দের আর ভারতীয়েরা সূফীদের প্রাণের সন্ধান লাভ করিলেন।
আইন-ই-আকবরীতে চৌদ্দটি সূফী খান্দান বা মণ্ডলীর উল্লেখ আছে। আবুল ফজল হয়তো প্রধান সম্প্রদায়গুলোরই নাম করেছেন। আমাদের অনুমানে তখন এক এক পীর-কেন্দ্রী এক এক সম্প্রদায় ছিল। পরে তাত্ত্বিক ও আচারিক বিধিবদ্ধ শাস্ত্র গড়ে উঠার ফলে সম্প্রদায়-সংখ্যা কমেছে এবং চারটি প্রধান মতবাদী খান্দান প্রসার লাভ করে। আর অপ্রধানগুলো কালে লোপ পায়, অথবা স্থানিক সীমা অতিক্রমণের যোগ্যতা হারায়। এ কারণেই আবুল ফজল কথিত চৌদ্দটি খান্দানের অনেকগুলোই লোপ পেয়েছে।
চিশতিয়া ও সুহরওয়ার্দিয়া মতই প্রথমে ভারতে তথা বাঙলায় প্রসার লাভ করে।৪৪ এরপরে নক্শবন্দিয়া এবং আরও পরে কাদিরিয়া সম্প্রদায় জনপ্রিয় হয়। মনে হয় ষোলো শতক অবধি চিশতিয়া, মদারিয়া ও কলন্দরিয়া সম্প্রদায়ের প্রভাবই বেশি ছিল। মদারিয়া ও কলন্দরিয়া মত একসময় জনপ্রিয়তা হারিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।
চৌদ্দ-পনেরো শতকের মধ্যেই সূফীর সর্বেশ্বরবাদ আর বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ অভিন্নরূপ নিল। আচার ও চর্যার ক্ষেত্রেও যোগপদ্ধতির মাধ্যমে ঐক্য স্থাপিত হল.। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এ অভিন্নতা প্রথম আমরা কবীরের (১৩৯৮-১৪৪৮) মধ্যেই প্রত্যক্ষ করি। এই মিলন-বিরোধী আন্দোলনও শতোকঁ বছর পর মুজদ্দদ-ই-আলফ-ই-সানী আহমদ সরহিন্দীর (১৫৬৩-১৬২৪) নেতৃত্বে গড়ে উঠে। কিন্তু সে-সংস্কার আন্দোলন সর্বব্যাপী হতে পারেনি। নকশবন্দিয়া এবং কিছুটা কাদিরিয়া। সম্প্রদায়েই এ সংস্কার আন্দোলন প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল। আলফসানী স্বয়ং একজন নকশবন্দিয়া।
বাঙলায় এ আন্দোলন দেশী তত্ত্ব চিন্তা ও চর্যার সঙ্গে ইসলামের বহির্বয়বের মিলন ঘটানোর চেষ্টায় পরিণতি লাভ করে। সৈয়দ সুলতান ও তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে এই প্রচেষ্টাই লক্ষ্য করি।
ভারতীয় যোগ-চর্যা ভিত্তিক তান্ত্রিক সাধনার যা-কিছু মুসলিম সূফীরা গ্রহণ করলেন, তাকে একটা মুসলিম আবরণ দেবার চেষ্টা হল, তা অবশ্য কার্যত নয় নামত। কেননা আরবি-ফারসি পরিভাষা গ্রহণের মধ্যেই এর ইসলামী রূপায়ণ সীমিত রইল। যেমন : নির্বাণ হল ফানা, কুণ্ডলিনীশক্তি হল নকশাবন্দিয়াদের লতিফা। হিন্দুতন্ত্রের ষড় পদ্ম হল এদের ষড় লতিফা বা আলোক-কেন্দ্র। এদেরও অবলম্বন হল দেহ চর্যা ও দেহস্থ আলোর উধ্বায়ন। পরম আলো বা মৌল আলোর দ্বারা সাধকের সর্বশরীর আলোময় হয়ে উঠে। এ হচ্ছে এক আনন্দময় অদ্বয়সত্তা-এর সঙ্গে সামরস্য জাত সহজাবস্থার, সচ্চিদানন্দ বা বোধিচিত্তাবস্থার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।
সূফীর জিকির ভারতিক প্রভাবে যোগীর ন্যাস, প্রাণায়াম ও জপের রূপ নিল। বর্হিভারতিক বৌদ্ধ-প্রভাবে (ইরানে, সমরখন্দে, বোখারায়-বলখে) এবং ভারতিক বৌদ্ধ-হিন্দু প্রভাবে বৌদ্ধ গুরুবাদও যোগতান্ত্রিক সাধকদের অনুসৃতি বশে সূফী সাধনায় অপরিহার্য হয়ে উঠল। সূফী মাত্রই তাই পীর-মুর্শিদ-নির্ভর তথা গুরুবাদী। গুরুর আনুগত্যই সাধনায় সিদ্ধির একমাত্র পথ। এটিই পরিণামে কবর পূজারও (দরগাহ্ বৌদ্ধ ভিক্ষুর স্তূপ পূজারই মতো হয়ে উঠল) রূপ পেল। সূফীরা আল্লাহর ধ্যানের প্রাথমিক অনুশীলন হিসেবে পীরের চেহারা ধ্যান করা শুরু করেন। শুরুতে বিলীন হওয়ায় অবস্থার উন্নীত হলেই শিষ্য আল্লাহতে বিলীন হওয়ার সাধনার যোগ্য হয়। প্রথম অবস্থার নাম ফানা-ফিশ-শেখ, দ্বিতীয় স্তরের নাম ফানা ফিল্লাহ। প্রথমটি রাবিতা (গুরুসংযোগ), দ্বিতীয়টি মুরাকিবাহু (আল্লাহর ধ্যান)। এই মুরাকিবায় যৌগিক পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। আসন, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি–এই চতুরঙ্গ যোগ পদ্ধতি থেকেই পাওয়া। পীরের খানকা বা আখড়ায়। সামা (গান), হালকা (ভাবাবেগে নর্তন), দারা (আল্লার নাম কীর্তনের আসর), হাল (অভিভূতি), সাকী, ইশক প্রভৃতি খাজা মঈনউদ্দীন চিশতীর আমল থেকেই চিশতিয়া খান্দানের সূফীদের সাধনায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে নিজামিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়েও এ রীতি গৃহীত হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় এরই অনুসৃতি রয়েছে।
সূফীদের দ্বারা দীক্ষিত অজ্ঞ জনসাধারণ শরীয়তী ইসলামের সঙ্গে ভাষার ব্যবধ্বন বশত অনেককাল পরিচিত হতে পারেনি। ফলে, তাহারা ক্রিয়াকলাপে আচার ব্যবহারে, ভাষায় ও লিখায়, সর্বোপরি সংস্কার ও চিন্তায় প্রায় পুরোপুরি বাঙালিই রহিয়া গেল। এমনকি হিন্দুত্বকে পুরোপুরি বর্জন করিতে পারিল না।
দরবেশদের প্রশ্রয়ও ছিল–তাহারা (দরবেশরা) কখনও বাহ্যিক আচার বিচারের প্রতি বিশেষ মনোযোগও দেনই নাই, এমনকি আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও অসাধারণ মহৎ ও উদার ছিলেন। …. এখনও পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গীয় শয়খ শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে অনেক হিন্দু ভাব, চিন্তা ও ব্যবহারের বহুল প্রচলন রয়েছে)। সাধারণ বঙ্গীয় মুসলমানদের মধ্যে এখনও তাহাদের ভারতীয় পিতৃপুরুষ হইতে লব্ধ বা পরবর্তীকালে গৃহীত যত হিন্দু ও বৌদ্ধ আচার ব্যবহার প্রচলিত আছে এবং চিন্তা ও বিশ্বাস ক্রিয়া করিতেছে।
বাঙলার ধর্ম
সাংখ্য ও যোগ –এই দুই শাস্ত্র ও পদ্ধতি যে আদিম অনার্য দর্শন ও ধর্ম তা আজকাল কেউ আর অস্বীকার করে না। এ শাস্ত্র অস্ট্রিক কিংবা বাঙলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের কিরাত জাতির মনন-উদ্ভূত, তা নিশ্চয় করে বলবার উপায় নেই। তবে উভয় গোত্রীয় লোকের মিশ্র-মননে যে এর বিকাশ এবং আর্যোত্তর যুগে যে এর সর্বভারতীয় তথা এশীয় বিস্তার, তা একরকম সুনিশ্চিত।
না বললেও চলে যে বাঙালি গোত্র-সঙ্কর বা বর্ণ-সঙ্কর জাতি। বাঙালির মধ্যে অস্ট্রিক প্রাধান্য থাকলেও ভোট-চীনার রক্তমিশ্রণ যে বহুল পরিমাণে ঘটেছে, তা নৃতাত্ত্বিক বিচারেই যে প্রমাণিত তা নয়, তাদের নানা আচার-আচরণেও দৃশ্যমান। বলতে কী বাঙালির দেহে আর্যরক্ত বরং দুর্লক্ষ্য। আর্য ধর্ম, সংস্কৃতি ও শাসনের প্রভাবেই আভিজাত্যকামী বাঙালি আর্যনামে পরিচিত।
বাঙালির শিব ও ধর্ম ঠাকুর অনার্য মানস প্রসূত। তেমনি অনাদি-আদিনাথও কিরাত জাতির দান। ভোট-চীনার নত, নথ, নাত, নাথ থেকেই যে নাথ গৃহীত, তা আজ আর গবেষণার অপেক্ষা রাখে না। অতএব নিষাদ-কিরাত অধ্যুষিত বাঙলায় বাঙালির ধর্ম ও সংস্কৃতির ভিত্তি এবং উদ্ভব রহস্য সন্ধান করতে হবে এই দুই গোত্রীয় মানুষের বিশ্বাস-সংস্কারে ও ভাষায়। মনে হয়, আর্য-পূর্ব যুগেই সাংখ্যদর্শন ও যোগপদ্ধতি সর্বভারতীয় বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এ কারণেই সম্ভবত ময়েনজো- দাড়োতেও যোগী-শিবমূর্তি আমরা প্রত্যক্ষ করি।
কোনো সংখ্যাল্প গোত্রের পক্ষেই বিদেশে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা সম্ভব হয় না। পৃথিবীর ইতিহাসেই রয়েছে তার বহু নজির। আমাদের দেশেই শক-হুঁন-ইউচি-তুর্কী-মুঘলেরা শাসক হিসেবেই এসেছিল, কিন্তু সংখ্যাল্পতার দরুনই হয়তো তারা তাদের ধর্ম ও ভাষা-সংস্কৃতি বেশি দিন রক্ষা করতে পারেনি। আর্যেরাও নিশ্চয়ই দেশবাসীর তুলনায় কম ছিল। তাই ঋগ্বেদেও মেলে দেশী ধর্ম-সংস্কৃতির প্রভাবের পরিচয়।
বৈদিক ভাষায় দেশী শব্দ যেমন গৃহীত হয়েছে, তেমনি যোগ-পদ্ধতিও হয়েছে প্রবিষ্ট। বস্তুত: এই দ্বিবিধ প্রভাব ঋগ্বেদেও সুপ্রকট। তাছাড়া, দেশী জন্মান্তরবাদ, প্রতিমা পূজা, নারী, পশু ও বৃক্ষদেবতার স্বীকৃতি, মন্দিরোপাসনা, ধ্যান এবং কর্মবাদ, মায়াবাদ এবং প্রেততত্ত্বও দেশী মনন প্রসূত। কাজেই যোগ ও তন্ত্র সর্বভারতীয় হলেও অস্ট্রিক নিষাদ ও ভোট-চীনা কিরাত অধ্যুষিত বাঙলা-আসাম-নেপাল অঞ্চলেই হয়েছিল এ-সবের বিশেষ বিকাশ। যোগীর দেহশুদ্ধি ও তান্ত্রিকের ভূতশুদ্ধি মূলত অভিন্ন এবং একই লক্ষ্যে নিয়োেজিত। বহু ও বিভিন্ন মননের ফলে, কালে ক্রমবিকাশের ধারায় সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র –তিনটে স্বতন্ত্র দর্শন ও তত্ত্বরূপে প্রতিষ্ঠা পায়। এবং প্রাচীন ভারতের আর আর ঐতিহ্যের মতো এগুলোও আর্য শাস্ত্র ও দর্শনের মর্যাদা লাভ করে।
অতি প্রাচীন শিব–কিরাতীয় ধানুকী, কৃষিজীবীর কৃষক এবং ব্রাহ্মণ্য যোগী তপস্বীরূপে নানা বিবর্তনে পৌরাণিক রূপ লাভ করেছেন বটে, কিন্তু তার আদিরূপও তথা বৃষ্টি, শস্য ও সন্তান উৎপাদনের (সূর্য) দেবতার স্মারকগুণও বিলুপ্ত হয়নি। বস্তুত দেবাধিদেব মহাদেবরূপে শিবকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় আর্য-অনার্য তত্ত্ব ও ধর্ম বিবর্তিত ও বিকশিত হয়েছে। তাই যোগ-পন্থের নায়কও শিব। তিনিই নাথপন্থের প্রভাবে হয়েছেন অনাদি, আদি ও চন্দ্রনাথ। এবং অন্যান্য নাথ সিদ্ধার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জনক।
এই যোগই শিব-সংপৃক্ত হয়ে বৌদ্ধ তান্ত্রিক, ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক, নাথ পন্থ, বৌদ্ধ সহজিয়া, বৈষ্ণব সহজিয়া [এ স্তরে শিব-উমার পরিবর্তে রাধাকৃষ্ণ প্রতীক গৃহীত] মতরূপে যেমন বিকাশ পেয়েছে, তেমনি সূফীমত সংশ্লিষ্ট হয়ে বাঙলার সূফীমত গড়ে তুলেছে। শৈবমতে ও নাথ-পন্থে পার্থক্য সামান্য ও অর্বাচীন। শিবত্ব, অমরত্ব ও ঈশ্বরত্ব তত্ত্বের দিক দিয়ে অভিন্ন। আজীবক, জিন, ব্রহ্মচারী, ভিক্ষু, সন্ন্যাসী, সন্ত এবং ফকিরও এ যৌগিক সাধনাকে অবলম্বন করে বৈরাগ্যবাদকে আজো চালু রেখেছে। আলেকজান্ডার, মেগাস্থিনিস, বার্দেনেস, হিউএন সাঙ, জালালুদ্দীন, আলবেরুনী, মার্কোপলো, ইবন-বতুতা প্রভৃতি সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে যোগীরা। এদিকে বেদে (সাম), ব্রাহ্মণে(শতপথ) ও উপনিষদে (ছান্দোগ্য), মহাভারতে, গীতায় ও পুরাণে যোগ, ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস প্রভৃতির প্রভাব ও উদ্ভব লক্ষ্য করা যায়। বৈদিক উপোসথ সম্ভবত যোগতত্ত্বের প্রভাবজ। শাসক ও সমাজপতি আর্যদের প্রাবল্যে হঙ্কার তথা ওঙ্কার মন্ত্র দিয়ে যৌগিক সাধনার শুরু হলেও, কুলবৃক্ষ বকুল, আভরণ রুদ্রাক্ষ ও কর্ণে কড়ি, আহার্য কচুশাক, শব সমাহিতি প্রভৃতি দেশী ঐতিহ্যেরই স্মারক।
মুণ্ডে আর হাড়ে তুমি কেনে পৈর মালা।
ঝলমল করে গায়ে ভস্ম, ঝুলি, ছালা।
পুনরপি যোগী হৈব কর্ণে কড়ি দিয়া। (গোরক্ষ বিজয়)
এই কড়িও অস্ট্রিক-দ্রাবিড়ের। মিশরেও ছিল এই কড়ির বিশেষ কদর। এখনো বাঙলার ও দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলের যোগীর কাছে কড়ি বিশেষ তত্ত্বের প্রতীক। শিবের এই রূপ নিশ্চিতই দেশী কিরাতের।
দেহাধারস্থিত চৈতন্যকেই তারা প্রাণশক্তি বা আত্মা বলে মানে। দেহনিরপেক্ষ চৈতন্য যেহেতু অসম্ভব, সেহেতু দেহ সম্বন্ধে তারা সহজেই কৌতূহলী হয়েছে। দেহ-যন্ত্রের অন্ধিসন্ধি বোঝা ও দেহকে ইচ্ছার আয়ত্তে রাখা ও পরিচালিত করাই হয়েছে তাদের সাধনার মুখ্য লক্ষ্য। তাই প্রাণ অপানবায়ু তথা শ্বাস-প্রশ্বাস বা রেচক-পূরক তত্ত্ব, দেহদ্বার, নাড়ি, দেহের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রভৃতির অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ তাদের পক্ষে আবশ্যিক হয়েছে। সেজন্য পরিভাষাও হয়েছে প্রয়োজন। এভাবে দশমী দুয়ার, চন্দ্র-সূর্য, ঈঙ্গলা-পিঙ্গলা-সুষুম্না, গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী, চতুশ্চক্র বা ষটচক্র, বিভিন্ন দল-সমন্বিত পদ্ম, বাঁকানল, কুলকুণ্ডলিনী, উলটা সাধনা প্রভৃতি নানা পরিভাষা ক্রমে চালু হয়েছে।
এই সাধনায় হঠ (রবি-শশী) যোগই মুখ্য অবলম্বন। হ-সূর্য বা অগ্নি, ঠ-চন্দ্র বা সোম। হঠ–শুক্র ও রজ:-র প্রতীক। এই যোগের বহুল চর্চা হয়েছে প্রাগজ্যোতিষপুরে, নেপালে, তিব্বতে ও বাঙলায়। বৌদ্ধ বজ্রযান, সহজযান, মন্ত্রযান ও তন্ত্রের প্রাণকেন্দ্র ছিল এই প্রাগজ্যোতিষপুরেরই কামরূপ-কামাখ্যা। এখানেই সংকলিত হয়েছিল প্রখ্যাত যোগগ্রন্থ অমৃতকুণ্ড। নেপাল ও তিব্বত আজো গুহ্যসাধকদের শিক্ষা ও প্রেরণার কেন্দ্র। [সিধ যোগী উতরাধী বা উত্যর দিসি সিধ কা জোগ–গোরখবাণী : ডক্টর পীতাম্বর দত্ত বড়ষ্যাল সম্পাদিত, পৃ. ১৬]।
অতএব এই কায়া-সাধন অতি প্রাচীন দেশী শাস্ত্র, তত্ত্ব ও পদ্ধতি। বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ্য ও মুসলিম বাঙালি তথা ভারতবাসী এর প্রভাব কখনো অস্বীকার করেনি। তবু নেপাল-তিব্বত ছাড়া সমভূমির মধ্যে বৌদ্ধযুগে কেবল বাঙলা দেশেই এর বিশেষ বিকাশ লক্ষ্য করি। কেননা এখানেই সহজিয়া ও নাথপন্থের উদ্ভব। এই বাঙলাদেশ থেকেই :
হাড়িকা পূর্বেতে গেল দক্ষিণ কানফাই
পশ্চিমেতে গোখ গেল উত্তরে মীনাই।
হাড়িসিদ্ধা ময়নামতীতে (চট্টগ্রামে-জালন ধারায়-সমরে?), কানুপা উড়িষ্যায়, মীননাথ। কামরূপ-কামাখ্যায় এবং গোরক্ষনাথ উত্তর-পশ্চিম ভারতে গিয়ে স্বমত প্রচার করেন। এদের মধ্যে গোরক্ষনাথের প্রভাবই সর্বভারতীয় হয়েছিল।
পূরবদেশ পছহী ঘাটি
[জন্ম] লিখ্যা হমারা জোঁগ।
গুরু হমারা নবগর কহী এ
মেটৈ ভরম বিরোগ [গোরখবাণী, ডক্টর পীতাম্বর দত্ত বড়থ্বাল সম্পাদিত, হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন, প্রয়াগ।]
–পূর্বদেশে (আমার] জন্ম, পশ্চিম দেশে বিচরণ, জন্মসূত্রে (আমি) যোগী, গুরু (আমার)ভব সাগরের নাবিক, আমি ভ্রমরূপ রোগ থেকে মুক্ত হই।
শেষ বয়সে সম্ভবত তিনি নেপালে অবস্থিত হন। নেপালীদের গোর্খা নাম হয়তো গোরক্ষনাথের প্রভাবের স্মারক। তাছাড়া গোরখপুর ও গোরখপন্থ আজো বিদ্যমান। মীননাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ তথা মোচংদরের প্রভাবও বিস্তৃতি পেয়েছিল। এঁদের প্রভাব, রচনা ও কাহিনী কেবল বাঙলা ভাষায় ও বাঙলা দেশেই বিশেষ করে রক্ষিত রয়েছে। বৌদ্ধ সহজিয়া পদ, বৈষ্ণব সহজিয়া গান, বাউল গীতি, যোগীর গান ও যুগী কাঁচ আজো বাঙলা দেশের সম্পদ। ভারতের অন্যত্র এসব গান ভক্তিবাদের মিশ্রণে বিকৃত।
এসব সিদ্ধার কেউ উচ্চবর্ণের লোক ছিলেন না। তাঁতী, তেলী, কৈবর্ত, ডোম, হাড়ি ও চাঁড়ালই ছিলেন।
ভণত গোরখনাথ মছিংদ্রণা পুতা [শিষ্য] জাতি হমারী তেলী
পীড়ি গোটা কাঢ়ি লীয়া পবন খলি দীয়া ঠেলী।
বদত গোরখনাথ জাতি মেরী তেলী।
তেল গোটা পীড়ি লীয়া খুলি দীবী মেলী।
—[গোরখবাণী, পিতাম্বর সম্পাদিত, পৃ. ১১৭]
এতেও এঁদের বাঙালিত্ব তথা অনার্যত্ব প্রমাণিত হয়।
এসব কায়াসাধকরা মানুষের জন্ম-রহস্য থেকে মৃত্যু-লক্ষণঅবধি সবকিছুর সন্ধান করেছেন এবং জিতেন্দ্রিয় হয়ে মৃত্যুঞ্জয় হবার উপায় আবিষ্কারে ব্রতী ছিলেন। দেহস্থ চারিচন্দ্র, শশাণিত, শুক্র, মল, মূত্র প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত ও স্বেচ্ছাচালিত করে অমৃতরসে পরিণত করতে চেয়েছেন। গুরুবাদী এ সাধনায় নাদ, বিন্দু, রজঃ ও শুক্র সৃষ্টিশক্তির উৎস। বিন্দু ধারণ করে সৃষ্টির পথ রুদ্ধ করলে, জীবনী-শক্তি অক্ষত থেকে আয়ুবৃদ্ধি করে। কেননা সৃষ্টিতেই শক্তির শেষ, সৃষ্টির পথ বন্ধ হলে ধ্বংসের পথও হয় রুদ্ধ। এভাবে তার ইন্দ্রিয় বা দেহের–
দশ দরজা বন্ধ হলে, তখন মানুষ উজান চলে।
স্থিতি হয় দশম দলে, চতুর দলে বারাম খানা।
বিন্দুর ঊর্ধ্বায়নের ফলে ললাট-দেশে তা সঞ্চিত হয়। এর নাম সহস্রার বা সহস্রদল পদ্ম। এতে চির রমণানন্দ লাভ হয়–এরই নাম সহজানন্দ বা সামরস্য। এই সহজানন্দের সাধকরাই সচ্চিদানন্দ, সহজিয়া ও আধুনিক বাউল।
চৈতন্যরূপ আত্মর রজ: ও শুক্ৰতেই স্থিতি। নতুন চৈতন্য সৃষ্টির জন্যে সে আত্মা রজ: ও শুক্র রূপে তরলতা প্রাপ্ত হয়। সাধক ও সাধিকা যথাক্রমে রজ:রক্ত ও শুক্রবিন্দু পান করে সেই চৈতন্যকে দেহধারে আবদ্ধ রাখে।
সর্বভারতীয় সাধনায় এবং ঐতিহ্যে পুষ্ট হয়েও সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র বাঙলার ধর্ম, বাঙালির ধর্ম। কেননা, এই ধর্মের উদ্ভব ও বিশেষ বিকাশভূমি বাঙলা। এখানেই অমৃতকুণ্ড, বৌদ্ধ সহজিয়ার দোহা ও চর্যাপদ, কৌলজ্ঞান নির্ণয়, বৈষ্ণব সহজিয়ার সহজিয়া পদ, বাউলগীতি, ধর্মমঙ্গল,শূন্যপুরাণ, ময়নামতী-মাণিকচন্দ্র-গোপীচাঁদ গাথা, যোগীপাল-ভোগীপাল-মহীপাল গীতি, গোরক্ষবিজয়, অনিলপুরাণ, যোগীর গান, যুগীকাঁচ, হাড়মালা, জ্ঞানপ্রদীপ, যোগকলন্দর, হর-গৌরী-সম্বাদ, নূরনামা, শির্নামা, তালিবনামা, আগম-জ্ঞানসাগর, আদ্যপরিচয়, নূরজামাল, গোৰ্থসংহিতা, যোগচিন্তামণি প্রভৃতি রচনা যেমন এদেশেই মেলে, তেমনি এদেশী লোকের ধর্ম-সাধনায় যোগতন্ত্র আজো অবিলুপ্ত। আজো হিন্দু-মুসলিম সমাজে প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধের সংখ্যা নগণ্য নয়। ডাকিনী-যোগিনী, তুক তাক, দারু-টোনা, মন্ত্র-কবচের জনপ্রিয়তাও বৌদ্ধপ্রভাবের স্মারক। গুরু, প্রেত আর যক্ষও বৌদ্ধদের দান। আজো বৌদ্ধ যোগ ও তন্ত্র বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের অধ্যাত্মসাধনার ভিত্তি। পাক ভারতের মধ্যে এদেশেই বৌদ্ধশাসন ও বৌদ্ধপ্রভাব ছিল দীর্ঘস্থায়ী–উত্তর-পশ্চিম বঙ্গে পাল-রাজত্ব ও পূর্বাঞ্চলে সমতটে চন্দ্র-শাসন। এখানেই অভিন্ন সত্তায় মিলেছে অস্ট্রিক-দ্রাবিড় ও ভোট-চীনার রক্ত, ধর্ম ও সংস্কৃতি। প্রাচীন কালেই নয় কেবল, মধ্যযুগে এবং আধুনিক কালেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও কলকাতার ব্রাহ্মমত বাঙালি ভারতবর্ষকে দান করেছে।
চৌরাশীসিদ্ধার অনেকেই বাঙালি। অবশ্য এই চৌরাশীসিদ্ধা সংখ্যাবাচক নয়, সিদ্ধিজ্ঞাপক। চৌরাশী আঙুল পরিমিত দেহতত্ত্বে সিদ্ধ–অর্থে মূলত চৌরাশীসিদ্ধা ব্যবহৃত [সৈয়দ সুলতানা। পরবর্তীকালে অজ্ঞতাবশে সিদ্ধার সংখ্যাজ্ঞাপক মনে হওয়ায় চৌরাশীজন সিদ্ধার তালিকা নির্মাণের ব্যর্থ প্রয়াস শুরু হয়েছে। ডক্টর সুকুমার সেনও মনে করেন, চৌরাশীদ্ধিা রূপকাত্মক। তিনি বলেন, চৌষট্টি যোগিনীর চৌষট্টির মতো চৌরাশীসিদ্ধের চৌরাশীও সাঙ্কেতিক সংখ্যামাত্র। [ড, পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত গোখাবিজয়-এর ভূমিকাস্বরূপ নাথ পন্থের সাহিত্যিক ঐতিহ্য প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য, পৃ. ১–খ(৬)।
মানুষের ধর্মমত কেবল আচার-আচরণই নিয়ন্ত্রণ করে না, তার ভাব-চিন্তাও পরিচালিত করে। এইজন্যে মানুষের সমাজ-সংস্কৃতিতে ও ভাব-চিন্তায় মতের প্রভাবই মুখ্য। বাঙালির এই যোগতান্ত্রিক জীবনতত্ত্বও বাঙালির জীবনে এবং মননে প্রগাঢ় ও ব্যাপক প্রভাব রেখেছে। এর ফলে বহিরাগত বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও ইসলাম এখানে কখনো স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এদেশীয় বিশ্বাস, সংস্কার ও আচারই বহিরাগত ধর্মমতের প্রলেপে বিকাশ ও বিস্তার পেয়েছে এবং কালিক অনুশীলনে ও বহু মননের পরিচর্যায় সূক্ষ্ম ও সুমার্জিত হয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে এনেছে উজ্জ্বল্য। এভাবে বৌদ্ধ-বিকৃতির ফলে পেলাম বজ্রযান, কালচক্রযান, মন্ত্রযান, সহজযান ও নাথপন্থ। ব্রাহ্মণ্যবিকৃতির পরিণামে পেলাম লৌকিক দেবতা ও তান্ত্রিক সাধনা, ইসলামী বিকৃতিতে এল সত্যপীর-কেন্দ্রী বহু দেবকল্প ও দেবপ্রতিদ্বন্দ্বী লৌকিক পীর–যাদের দু-চারজন সেনানী শাসক হলেও অধিকাংশ ব্যক্তিত্ব কাল্পনিক। আজো আমাদের সামাজিক, পার্বণিক ও আচারিক রীতিনীতিতে আদিম Animism, Magic-belief প্রবল ও মুখ্য। আমাদের ধর্মীয় বিশ্বাস কেবল বহিরাঙ্গিক প্রসাধনের মতোই আমাদের পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্য ও রিখতের সঙ্গে প্রলিপ্ত হয়ে আছে মাত্র। তাই ডক্টর সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ধারণা আক্ষরিকভাবেই সত্য। তিনি বলেন :
It is now becoming more and more clear that the Non-Aryan contributed by far the greater portion in the fabric of Indian civilization, and a great deal of Indian religious and cultural traditions, of ancient legend and history, is just non-Aryan translated in terms of the Aryan speech …… the ideas of Karma and transmigration, the practice of Yoga, the religious and philosophical ideas centring round the conception of the divinity as Siva and Devi and as Vishnu, the Hundu ritual of Puja as opposed to the Vedic ritual of Homa-all these and much more in Hindu religion and thought would appear to be non-Aryan in origin, a great deal of Puranic and epic myth, legend and semi-history is Pre-Aryan, much of our material culture and social and other usages, eg. the cultivation of some of our most important plants like rice and some vegetables and fruits like tamarind and the coconut etc., the use of betel leaf in Hindu life and Hindu ritual, most of our popular religion, most of our folk crafts, our nautical crafts, our distinctive Hindu dress (the dhoti and sari), our marriage ritual in some parts of India with the use of vermilion and turmeric and many other things would appear to be legacy from our Pre-Aryan ancestors.
[ Indo-Aryan and Hindi PP. 31-32]
যোগ ও তান্ত্রিক সাধনা দ্বিবিধ : বামাচারী ও কামাচার বর্জিত। গোরক্ষনাথ কামাচারবর্জিত বা ব্রহ্মচর্য সাধনার প্রবর্তক। এ গোরক্ষমতবাদীরাই নাথপন্থী। আর হাড়িফা বা জ্বালন্ধরী পাদ অনুসারীরা বামাচারী। প্রথমোক্ত সম্প্রদায় অবধূত যোগী, শেষোক্ত সম্প্রদায় কাঁপালিক যোগী। নাথপন্থীরা পরিণামে ব্রাহ্মণ্য শৈবদের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে উঠে। আর পা-পন্থীরাও শৈব-শাক্ত তান্ত্রিকরূপে ব্রাহ্মণ্য সমাজভুক্ত হয়ে পড়ে। মূলত এদের সাধনা আজো প্রচ্ছন্ন ও বিকৃত বৌদ্ধমত ভিত্তিক তথা আদি সাংখ্য-যোগ-তন্ত্র-ধারার ধারক। পরিণামে সবাই আত্মজ্ঞান, শিবত্ব, অমরত্ব ও মোক্ষ-কামী। এদেশের প্রাচীন অনার্য শিব ভোট-চীনার প্রভাবে নাথ হয়ে আবার ব্রাহ্মণ্য-প্রাবল্যে শিব-হর-মহাদেব রূপে পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত হন। তাই আদিম, প্রাচীন ও অর্বাচীন তথা দ্রাবিড়, অস্ট্রিক, মোঙ্গল ও আর্য-মনন প্রসূত সব দ্বান্দ্বিক গুণ নিয়ে শিব আজো জীবন্ত উপাস্য দেবতা।
দেহস্থিত চৈতন্যই আত্মা। এ আত্মা জগৎ-কারণ পরমাত্মারই অংশ। খণ্ডকে স্বরূপে জানলে অখণ্ডকেও জানা হয়ে যায়। এজন্যে দেহের কর্তৃত্ব বা নিয়ন্ত্রণাধিকার চাই। এই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব দম বা শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ পবন যখন আয়ত্তে আসে। আর এজন্যে বিন্দুধারণ, দেহ বা ভূতশুদ্ধি, ত্রিকাল দৃষ্টি, ভাণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডও জীবে ব্রহ্মদর্শন, আত্মজ্ঞান, ইচ্ছাসুখ, ইচ্ছামৃত্যু প্রভৃতির সামর্থ্য অর্জন প্রয়োজন।
দেহ হচ্ছে মন-পবনের নৌকা। প্রাণ ও অপান বায়ু আর মনরূপে অভিব্যক্ত চৈতন্যই হচ্ছে দেহযন্ত্রের ধারক ও চালক। তাই মন-পবনকে যৌগিক সাধনা বলে ইচ্ছাশক্তির আয়ত্তে আনতে হয় :
মনথির তো বচন থির
পবন থির তো বিন্দু থির
বিন্দু থির তো কন্ধ থির
বলে গোরখদেব সকল থির।
[ অক্ষয় কুমার দত্ত ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়, ২য় খণ্ড, ২য় সং, পৃ. ১১৮।
বাঙালি মুসলমানেরা এই সাধনাই বরণ করেছিল। কেবল দু-চারটা আরবি-ফারসি পরিভাষা এবং আল্লাহ্-রসুল, আদম-হাওয়া, মোহাম্মদ, খাদিজা, আলি-ফাতেমা এবং রাকিনী প্রভৃতি বদলে ফিরিস্তা বসিয়ে এই প্রাচীন কায়া-সাধনাকে ইসলামী রূপ দানে প্রয়াসী ছিল। সমন্বয়ের চেষ্টাও আছে। যেমন নয়ানচাঁদ ফকীরের বালকানামায় পাই :
দিলসে বৈঠে রাম-রহিম দিলসে মালিক-সাঁই।
দিলসে বৃন্দাবন মোকাম মঞ্জিল স্থান তেস্ত পাই।
ঘরে বৈঠে চৌদ্দ ভূবন মুজিআ আলম তারা
চাঁদযুক্ত মেঘজুতি ইন্দ্রে বইছে ধারা। ….. [ প্রাচীন পুঁথির বিবরণ : আবদুল করিম ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, পৃ. ১৩৮]
অতএব, বাঙলার ও বাঙালির আদিধর্ম বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও ইসলামী আবরণে আজকের দিনেও অবিলুপ্ত। ধর্ম, আদ্য, পুরুষপুরাণ, নাথ ও নিরঞ্জন–পাক-ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাঙলা দেশেও আল্লাহ্-খোদার পরিভাষারূপে গোটা মধ্যযুগে বহুল ব্যবহৃত হয়েছে।
যোগ ও তন্ত্রের বিশেষ বিকাশ ঘটে বৌদ্ধযুগে এবং বৌদ্ধ সমাজের ক্রমবিলুপ্তিতে গড়ে উঠে বাঙলার ব্রাহ্মণ্য ও মুসলিম সমাজ। তাই পূর্ব ঐতিহ্যের ও বিশ্বাসের রেশ রয়েছে তাদের মননে ও আচারে।
এরও আগে পাই মৃগয়াজীবী ও মাতৃপ্রধান সমাজের কৃষিজীবী ও পিতৃপ্রধান সমাজে রূপান্তরের ইঙ্গিত। বাঙলায় নারীদেবতার আধিক্য মাতৃপ্রাধান্যের সাক্ষ্য এবং ক্ষেত্ৰপ্রাধান্যও তারা, শাকম্ভরী (দুর্গা), বসুমতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতির জনপ্রিয়তায় সপ্রমাণ। তাছাড়া মৃগয়াজীবীর হাতিয়ার হরধনু ভঙ্গ করে তথা পরিহার করে রাম কর্তৃক সীতাকে লাঙ্গলের ফাল] গ্রহণ কিংবা অহল্যাকে (যাতে হল পড়েনি] প্রাণ দান প্রভৃতি রূপকের মধ্যেও রয়েছে কিরাতীয় নিষাদীয় যাযাবর জীবন থেকে স্থির নিবিষ্ট কৃষিজীবনে উত্তরণের ইতিহাস।
জীবিকার ক্ষেত্রে এই মৃগয়াও কৃষিজীবনের অসহায়তার অভিজ্ঞতা থেকেই আসে যাদুতত্ত্বে ও জন্মান্তরবাদে আস্থা। কেননা, তারা অনুভব করেছে বাঞ্ছসিদ্ধির পথে কোথা থেকে যেন কী বাধা আসে। কার্য-কারণ জ্ঞানের অভাবে এ প্রতিকূল্য কিংবা আনুকূল্যের অদৃশ্য অরি ও মিত্রশক্তি সে কল্পনা না করে পারেনি। তাই প্রতিকার-প্রতিরোধ কিংবা আবাহন মানসে সে আস্থা রেখেছে যাদুতে, মন্ত্রশক্তিতে, পূজায় এবং প্রতীকী ও আনুষ্ঠানিক আবহে।
অভিজ্ঞতা থেকে সে জেনেছে বীজে বৃক্ষ, বৃক্ষে ফল এবং ফলে বীজ আবর্তিত হয়–ধ্বংস হয় না। সে বীজও বিচিত্র–কখনো দানা, কখনো শিকড়, কখনো কাণ্ড, আবার কখনো বা পাতা। কাজেই প্রাণ ও প্রাণীর আবর্তন আছে, বিবর্তনও সম্ভব–কিন্তু ধ্বংস যেন অসম্ভব। এর থেকেই হয়তো উদ্ভূত হয়েছে আত্মা ও আত্মার অবিনশ্বরত্বের তত্ত্ব।
আবার, অদৃশ্য অরি কিংবা মিত্রশক্তির সঙ্গে সংলাপের ভাষা নেই বলে সে প্রতাঁকের মাধ্যমে জানতে চেয়েছে তার প্রয়োজনের কথা এবং তার ভয়, বাঞ্ছা ও কৃতজ্ঞতা। তার এই অনুযোগ ও প্রার্থনা নিবেদিত হয়েছে নাচে, মুদ্রায়, গানে ও চিত্রে এবং প্রতীকী বস্তুর উপস্থাপনায়। এভাবে তার প্রাণের ও আয়ুর প্রতীক হয়েছে দূর্বা, খাদ্যকামনার প্রতীক হয়েছে ধান, সন্তানবাঞ্ছা অভিব্যক্তি পেয়েছে মাছের প্রতাঁকে, কলাগাছের রূপকে প্রকাশ পায় বৃদ্ধির কামনা, আম্রকিশলয় তার জরা ও জ্বরমুক্ত স্বাস্থ্যের ও যৌবনের প্রতীক, আর পূর্ণকুম্ভ হচ্ছে সিদ্ধির ও সাফল্যের প্রতীকী কামনা।
মূলত সব বিশ্বাস-সংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান ও শিল্প-সংস্কৃতির জন্ম হয় আঞ্চলিক প্রতিবেশপ্রসূত জীবন-চেতনা ও জীবিকাপদ্ধতি থেকেই। তাই বৈষয়িক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা, জীবিকা পদ্ধতি এবং পরিবেষ্টনীজাত ভূয়োদর্শন থেকেই সৃষ্টি হয় প্রবাদ-প্রবচনাদি আপ্তবাক্যের এবং উপমা, রূপক ও উৎপেক্ষার।
কালে এগুলোই হয়ে উঠল জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে লোকশিক্ষার উৎস ও আধার এবং পরিণামে এগুলোই হল ধার্মিক, নৈতিক, বৈষয়িক ও সামাজিক জীবনের নিয়ামক। এরই আধুনিক নাম শাস্ত্রীয় বিশ্বাস, সামাজিক সংস্কার, নৈতিক চেতনা ও জাগতিক প্রজ্ঞা। মননের বৃদ্ধি ও ঋদ্ধির ফলে এর কোনো কোনটি দার্শনিক তত্ত্বের মর্যাদায় উন্নীত। যেমন যাদুতত্ত্বের উত্তরণ ঘটেছে অধ্যাত্মতত্ত্বে। জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা প্রাপ্তির প্রেরণাবশে যে-ভাব, চিন্তা ও কর্মের উদ্ভাবন, পরিবর্তিত প্রতিবেশে ক্রমবিকাশের ধারায় কালে তা-ই ধর্ম, দর্শন, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও মানবতারূপে পরিকীর্তিত। যে-কোনো সংস্কার অকৃত্রিম বিশ্বাসে পুষ্ট ও প্রবল হয়ে ধর্মীয় প্রত্যয়ে পায় পরিণতি ও স্থিতি।
অতএব, বাঙলার এই ধর্ম প্রবর্তিত ধর্ম নয়–লোকায়ত লোকধর্ম। ভৌগোলিক প্রভাবে ও ঐতিহাসিক কারণে সমাজ বিবর্তনের ধারায় এর কালিক সৃষ্টি ও পুষ্টি সম্ভব হয়েছে। এ ধর্ম গোষ্ঠীর তথা সামাজিক মানুষের যৌথজীবনের দান–জনমানবের জীবনচেতনা ও জীবিকাপদ্ধতির প্রসূন। গণ মন-মননের রসে সঞ্জীবিত গণ-সংস্কৃতির প্রমূর্ত প্রকাশ। এই ধর্ম ও সংস্কারের এবং আচার ও অনুষ্ঠানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে প্রাচীন বাঙালির পরিচয় ও আধুনিক বাঙালির ঐতিহ্য। ইতিহাসের আলোকে স্বরূপে আত্মদর্শন করতে হলে এসবের সন্ধান আবশ্যিক।
বাঙালির ধর্মতত্ত্বে পাপ-পুণ্যের কথা বেশি নেই। অনেক করে রয়েছে জীবন-রহস্য জানবার ও বুঝবার প্রয়াস। লোক-জীবনে সে-প্রয়াস আজো অবিরল। মনে হয় দারিদ্রক্লিষ্ট লোক-জীবনের যন্ত্রণামুক্তির অবচেতন অপপ্রয়াসে অসহায় মানুষ অধ্যাত্মতত্ত্বে স্বস্তি ও শক্তির, প্রবোধ ও প্রশান্তির প্রশ্রয় কামনা করেছে। এভাবে পার্থিব পরাজয়ের ও বঞ্চনার ক্ষোভ ও বেদনা ভুলবার জন্যে আসমানী-চিন্তার মাহাত্ম-প্রলেপে বাস্তবজীবনকে আড়াল করে ও তুচ্ছ জেনে মনোময় কল্পনোক রচনা করে এই নির্মিত ভুবনে বিহার করে আনন্দিত হতে চেয়েছে দুস্থ ও দুঃখী মানুষ। আজো গরিবঘরের প্রতারিত-বঞ্চিত সেই মানুষ উদারকণ্ঠে সেই উদাস গান গায়। তার জৈব প্রয়োজনের সামগ্রীই হয়েছে তার সেই ভাবের জীবনের রূপক। এ-ই হয়তো দুঃখ দীর্ণ, দ্বন্দ্ব-ভীরু পলাতক মনের অভয় আশ্রয়, হয়তো বা পিছিয়ে-পড়া মানুষের প্রতিহত কাম্যজীবনের স্বাপ্নিক প্রকাশ অথবা আত্মপ্রত্যয়হীন মানুষের অবচেতন কামনার বিদেহী গুঞ্জন।
বাঙালির সংস্কৃতি
অন্যান্য প্রাণী ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য এই যে, অন্য প্রাণী প্রকৃতির অনুগত জীবন ধারণ করে আর মানুষ নিজের জীবন রচনা করে। প্রকৃতিকে জয় করে, বশীভূত করে প্রকৃতির প্রভু হয়ে সে কৃত্রিম জীবন যাপন করে– এ-ই তার সংস্কৃতি ও সভ্যতা। অতএব, এইভাবে জীবন রচনা করার নৈপুণ্যই সংস্কৃতি। স্বল্প কথায় সুন্দর ও সামগ্রিক জীবনচেতনাই সংস্কৃতি। চলনে-বলনে, মনে-মেজাজে, কথায়-কাজে, ভাবে-ভাবনায়, আচারে-আচরণে অনবরত সুন্দরের অনুশীলন ও অভিব্যক্তিই সংস্কৃতিবানতা। সংস্কৃতিবান ব্যক্তি অসুন্দর, অকল্যাণ ও অপ্রেমের অরি। সুরুচি ও সৌজন্যেই তাই সংস্কৃতিবানতার প্রকাশ। সংস্কৃতিবান মানুষ কখনও জ্ঞাতসারে অন্যায় করে না, অল্যাণকর কিছুকে প্রশ্রয় দেয় না, অপ্রীতিতে বেদনাবোধ করে এবং কৌৎসিত্যকে সহ্য করে না। অন্য কথায়, যেখানে কথার শেষ সেখানেই সুরের আরম্ভ, যেখানে Photography-র শেষ সেখান থেকেই শিল্পের শুরু, নক্সার উধ্বেই সাহিত্যের স্থিতি, তেমনি যেখানে স্কুল জৈব প্রয়োজনের শেষ, সেখান থেকেই সংস্কৃতির শুরু। সংস্কৃতিবান মানুষ জ্ঞানে-প্রজ্ঞায়, অভিজ্ঞতায় ও প্রয়োজনবোধে চালিত হয়ে অনবরত জীবনকে রচনা করতে থাকে এবং পরিবেশকে স্নিগ্ধ ও সুন্দর করবার প্রয়াসী হয়। এজন্যে সংস্কৃতিবান ব্যক্তিমাত্রেই কেবল নিজের প্রতি নয়, প্রতিবেশীর প্রতিও নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্বীকার করে। এবং সচেতনভাবে ও সযত্নে নিজেকে সুন্দর করে, সৃষ্টি করে এবং নিজের আচারে আচরণে, মনে-মননে, কথায়-কাজে অপরের পক্ষে স্মরণীয়, বরণীয়, অনুকরণীয়, অনুসরণীয় ও আকর্ষণীয় লাবণ্য ছড়িয়ে তৈরি করে প্রতিবেশীদের সুষ্ঠু জীবনের ভিত্।
বীজের আত্মবিকাশের জন্যে যেমন কৰ্ষিত ক্ষেত্র প্রয়োজন, সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশের জন্যেও তেমনি সুকর্ষিত মনোভূমি তথা পরিস্রত চেতনা আবশ্যক। তাই সংস্কৃতির স্রষ্টামাত্রেই বিজ্ঞ ও বিবেকবান, সুন্দরের ধ্যানী ও আনন্দের অন্বেষ্টা, বুদ্ধি ও বৃদ্ধির সাধক,মঙ্গল ও মমতার বাণীবাহক এবং প্রীতি ও প্রফুল্লতার উদ্ভাবক।
চরিত্রবল, মুক্তবুদ্ধি ও উদারতার ঐশ্বর্যই এমন মানুষে সম্বল ও সম্পদ। বেদনা-মুক্তি ও আনন্দ-অন্বেষাই মানুষের জীবনসত্য। এক্ষেত্রে সিদ্ধির জন্যে প্রয়োজন সুন্দর ও কল্যাণের প্রতিষ্ঠা। আর এই সৌন্দর্য-অন্বেষা ও কল্যাণকামিতাই সংস্কৃতি। . মানুষের জীবনে সম্পদ ও সমস্যা, আনন্দ ও যন্ত্রণা পাশাপাশি চলে, বলা যায় একটি অপরটির সহচর। কিন্তু এগুলো যখন আনুপাতিক ভারসাম্য হারায়, তখন সুখ কিংবা দুঃখ বাড়ে। সুখ বৃদ্ধি পেল তো ভালই, কিন্তু সমস্যা ও যন্ত্রণার চাপে যখন জীবন-জ্বালা আত্যন্তিক হয়ে উঠে, তখনই বিচলিত-বিপর্যস্ত মানুষ স্বস্তি কামনায় সমাধান খোঁজে। এ সমাধান দিতে পারেন এবং দেনও কেবল সংস্কৃতিবান মানুষই।
মানুষ মাত্রেই সচেতন কিংবা অবচেতনভাবে সংস্কৃতিকামী। কিন্তু সাধনার মাত্রা ও পথ পদ্ধতি সবার এক রকম নয়। তাই সংস্কৃতিতে আসে গৌত্রিক, আঞ্চলিক, সামাজিক, আর্থিক ও আত্মিক বৈষম্য ও বিভিন্নতা। এবং স্তরভেদে তা হয় নিন্দনীয় কিংবা বন্দনীয়, অনুকরণীয় কিংবা পরিহার্য।
আগের কথা জানিনে, কিন্তু ইতিহাসান্তৰ্গত যুগে দেখতে পাই বাঙালি মনোভূমি কর্ষণ করেছে সযত্নে। এবং এই কর্ষিত ভূমে মানবিক সমস্যার বীজ বপন করে সমাধানে ফল ও ফসল পেতে হয়েছে উৎসুক। এই এলাকায় বাঙালি অনন্য। এ যেন তার নিজের এলাকা, সে এই মাটিকে। ভালবেসেছে, সে এ জীবনকে সত্য বলে জেনেছে। তাই সে দেহতাত্ত্বিক, তাই সে প্রাণবাদী, তাই সে যোগী ও অমরত্বের পিপাসু। এজন্যেই নির্বাণবাদী বুদ্ধের ধর্মগ্রহণ করেও সে কায়া সাধনায় নিষ্ঠ। তার কাছে এ মর্ত্যজীবনই সত্য, পারত্রিক জীবন মায়া। মর্ত্যজীবনের মাধুর্যে সে আকুল, তাই সে মর্ত্যে অমৃতসন্ধানী। সে বিদ্রোহী, সে বলে :
কিংতো দীবে কিংতো নিবেজেঁ
কিংতো কিজ্জই মন্তহ সেব্ব।
কিংতো তিথ-তপোবন জাই।
মোখক কী লবভই পানী হ্নাই।
–কী হবে তোর দীপে আর নৈবেদ্যে? মন্ত্রের সেবাতেই বা কী হবে তোর, তীর্থ-তপোবনই। বা তোকে কী দেবে? পানিতে স্নান করলেই কী মুক্তি মেলে?
অনেককাল পরে এই ধারারই সাধক বাউলের মুখে শুনতে পাই :
সখিগো, জন্ম মৃত্যু যাহার নাই।
তাহার সনে প্রেম গো চাই।
উপাসনা নাই গো তার
দেহের সাধন সর্বসার।
তীর্থব্রত যার জন্য
এ দেহে তার সব মিলে।
জীবনবাদী বাঙালি তাই বৌদ্ধ হয়েও মর্ত্যের জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তার বাঞ্ছায় অসংখ্য উপ ও অপদেবতার সৃষ্টি ও পূজা করেছে। সাংখ্যকেই সে তার দর্শনরূপে এবং যোগকেই তার সাধনপদ্ধতি রূপে গ্রহণ করেছে। তন্ত্রকেই সার বলে মেনেছে। দেহে-মনে আত্ম-অধিকার প্রতিষ্ঠাকেই। জীবনকাঠি বলে জেনেছে। আর যোগ-তান্ত্রিক কায়া-সাধনার মাধ্যমে সে কামনা করেছে দীর্ঘ জীবন ও অমরত্ব। এ জীবনকে সে প্রত্যক্ষ করেছে চলচঞ্চল ও তরঙ্গভঙ্গে লীলাময় মন-পবনের নৌকারূপে। বৌদ্ধ যুগে তার সাধনা ছিল নির্বাণের নয়–বাঁচার, কেবল মাটি আঁকড়ে বাঁচার। মন ভুলানো ভুবনের বনে বনে, ছায়ায় ছায়ায়, জলে-ডাঙায় ভালবেসে, প্রীতি পেয়ে মমতার মধুর অনুভূতির মধ্যে বেঁচে থাকার আকুলতাই প্রকাশ করেছে সে জীবনব্যাপী। হরগৌরীর মহাজ্ঞান, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, হাড়িফা-কানুফা, ময়নামতী-গোপীচাঁদ প্রভৃতির কাহিনীর মধ্যে আমরা এ তত্ত্বই পাই। অবশ্য এ বাঁচা স্কুল ও জৈবিক ভোগের মধ্যে নয়, ত্যাগের মধ্যে সূক্ষ্ম, সুন্দর ও সহজ মানসোপভোগের মধ্যে বাঁচা। কিন্তু এই জীবন-সত্যে সে কী নিঃসংশয় ছিল?–মনে হয় না। তাই বিলুপ্ত যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপাল গীতে তার দ্বিধা ও মানস-দ্বন্দ্বের আভাস পাই। পাল আমলের গীতে মনে হয়, সে মধ্যপন্থা (golden mean) অবলম্বন করেছে। যোগেও নয়, ভোগেও নয়, মর্ত্যকে ভালবেসে দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যেই যেন সে বাঁচতে চেয়েছে, চেয়েছে জীবনকে উপলব্ধি ও উপভোগ করতে। তার সেই জানা-বোঝার সাধনায় আজও ছেদ পড়েনি। বাউলেরা তাই গৃহী, যোগীরা তাই অমরত্বের সাধক, বৈষ্ণব বৈরাগীরা তাই ঘর করে, আর ফকিরেরা বাঁধে ঘর।
সেন আমলে এখানে ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রবল হয়। লুপ্তপ্রায় বৌদ্ধসমাজ বর্ণে বিন্যস্ত হয়ে বল্লালসেনের নেতৃত্বে উগ্র ব্রাহ্মণ্য সমাজ গড়ে তোেলে। কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি। গীতা-স্মৃতি উপনিষদের মত সে মুখে গ্রহণ করলেও মনে মানেনি। তার ঠোঁটের স্বীকৃতি বুকের বাণী হয়ে উঠেনি। কেননা সে ধার করে বটে, কিন্তু জীবনের অনুকূল না হলে অনুকরণ কিংবা অনুসরণ করে না। তাই সে তার প্রয়োজনমতো জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তার প্রতীক দেবতা সৃষ্টি করে পূজা করেছে, আশ্বস্ত হতে চেয়েছ ঘরোয়া ও মানস জীবনে। তার মনসা, চণ্ডী, শীতলা, ষষ্ঠী, শনি তার স্বসৃষ্ট দেবতা। জীবনের সামাজিক সমস্যার সমাধানে ও অধ্যাত্মজীবনের বিকাশ সাধনে সে আরো এগিয়ে এসেছে। জীমূতবাহন ও বল্লালসেন, রঘুনাথ, রামনাথ প্রভৃতির স্মৃতি ও ন্যায় দৈবকী বানন্দ-পঞ্চাননের মেল-পটি প্রভৃতি গোত্র ও বর্ণবিন্যাস প্রয়াস, চৈতন্যের ভগবৎপ্রেম ও মানব প্রীতিবাদ বাঙালি জীবনে রেনেসাঁস আনে। এবং তার প্রসাদে আপামর বাঙালির দেহ-মন-আত্মা গ্লানিমুক্ত হয়। এ নতুন কিছু ছিল না, গৌতমের করুণা ও মৈত্রীতত্ত্বের ঐতিহ্যে সূফীমতের প্রভাবেই মানব-মহিমা বাঙালি চিত্তে নতুন মূল্যে ও ঔজ্জ্বল্যে প্রতিভাত হয়। বাঙালি নতুন করে জীবে ব্রহ্ম এবং নরে নারায়ণ দর্শন করে। তখন বাঙালির মুখে উচ্চারিত হয় মানুষের মর্যাদা ও মনুষ্যত্বের মহিমা চণ্ডালেহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ।–মানবিক সম্ভাবনার এ স্বীকৃতি সেদিন জীবন-বিকাশের নিঃসীম দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে। তাই বাঙালির কণ্ঠে আমরা সেদিন শুনতে পেয়েছিলাম চরম সত্য ও পরম কাম্য বাণী–শুনহ মানুষ ভাই, সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।
বাঙালি এই ঐতিহ্য আজও হারায়নি। আজো হাটে-ঘাটে-প্রান্তরে বাউলকণ্ঠে সেই বাণী শুনতে পাই। মানববাদী বাউলেরা আজো উদাত্তকণ্ঠে মানুষকে মিলন-ময়দানে আহ্বান জানায়, আজো তারা মানবতার শ্রেষ্ঠ সাধক ও চিন্তানায়কের কণ্ঠের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে সাম্য, সহঅবস্থান ও সম্প্রীতির বাণী শোনায়। তারা বলে :
নানা বরণ গাভীরে ভাই
একই বরণ দুধ
জগৎ ভরমিয়া দেখিলাম
একই মায়ের পুত।
কাজেই কাকেই বা দূরে ঠেলবি আর কাকেই বা কাছে টানবি! তোরা তো ভাই ফুল কুড়োতে কেবল ভুলই কুড়োচ্ছিস। কৃত্রিম বাছ-বিচারের ধাঁধায় কেবল নিজেকেই ঠকাচ্ছিস। গোত্রীয়, ধর্মীয় ও দেশীয় চেতনা বিভেদের প্রাচীরই কেবল তৈরি করেছে বিদ্বেষ ও বিবাদ সৃষ্টি করেছে, হানাহানির প্রেরণাই কেবল দিয়েছে, তাই বাউল বলেন :
যদি
সুন্নত দিলে হয় মুসলমান।
নারী লোকে কী হয় বিধান?
বামুন চিনি পৈতার প্রমাণ
বামনী চিনি কী করে?
একালের ইংরেজি শিক্ষিত কবি যখন বলেন :
সবারে তুই বাসরে ভাল, নইলে তোর মনের কালি ঘুচবে না রে।
কিংবা –
কালো আর ধলো বাহিরে কেবল
ভিতরে সবার সমান রাঙা
অথবা,–
গাহি সাম্যের গান।
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই।
নহে কিছু মহীয়ান;
তখন তা আমাদের কাছে নতুন ঠেকে না। কেননা প্রকৃত বাঙালির অন্তরের বাণী স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হতে দেখেছি আমরা কত কত কাল আগে।
ওহাবী-ফরায়েজী আন্দোলনের পূর্বে এখানে শরীয়তী ইসলামও তেমন আমল পায়নি। একপ্রকার লৌকিক তথা দেশজ ইসলামই লোকের অবলম্বন হয়েছিল। তখন পার্থিব জীবনের স্বস্তির ও জীবিকার নিরাপত্তার জন্য কল্পিত হয়েছিলেন দেব-প্রতিম পাঁচগাজী ও পাঁচপীর। নিবেদিত চিত্তের ভক্তি লুটেছে খানকা, অর্ঘ্য পেয়েছে দরগাহ্ আর শিরনী পেয়েছেন দেশের সেনানী-শাসক জাফর-ইসমাইল-খান জাহান-গাজীরা এবং বিদেশাগত বদর-আলম-জালাল-সুলতান প্রভৃতি সুফীরা, তার পরেও প্রয়োজন হয়েছিল সত্যপীর-খিজির-বড়খা-গাজী-কালু-বনবিবি-ওলাবিবি প্রভৃতি দেবকল্প কাল্পনিক পীরের। এঁরা বাঙালির ঐহিক জীবনের নিয়ন্তা দেবতা। জীবনবাদী বাঙালি এঁদের উপর ভরসা করেই সংসার-সমুদ্রে ভাসাত জীবন-নৌকা। এখানেই শেষ নয়। চিন্তাজগতে বাঙালি চিরবিদ্রোহী। বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ও মুসলিম ধর্ম সে নিজের মতো করে গড়তে গিয়ে যুগে যুগে সে চিন্তাজগতে বিপ্লব ঘটিয়েছে। বাহ্যত সে ভাববাদী হলেও, উপযোগ-তত্ত্বেই তার আস্থা ও আগ্রহ অধিক।– বৌদ্ধযুগে বৌদ্ধ বজ্রমান-সহজযান-কালচক্রযান, থেরবাদ, অবলোকিতেশ্বর ও তারা দেবতার প্রতিষ্ঠা এবং যোগতান্ত্রিক সাধনায় বিকাশ সাধন করে সে তার স্বকীয়তার, সৃষ্টিশীলতার, মনন বৈচিত্র্যের ও স্বাতন্ত্রের স্বাক্ষর রেখে গেছে।
ব্রাহ্মণ্যযুগে জীমূতবাহন, বল্লালসেন, রামনাথ, রঘুনাথ, রঘুনন্দন প্রভৃতি নবস্মৃতি ও নবন্যায় সৃষ্টি করে তাঁদের চিন্তার ঐশ্বর্যে ও প্রজ্ঞার প্রভায় জ্ঞানলোক সমৃদ্ধ ও উজ্জ্বল করেছেন।
মুসলিম আমলে চৈতন্যদেবের নবপ্রেমবাদ, সত্যপীর-কেন্দ্রী নবপীরবাদ, চাঁদ সদাগরের আত্মসম্মানবোধ ও তেজস্বিতা, বেহুলার বিদ্রোহ ও কৃচ্ছ্ব-সাধনা, গীতিকায় পরিব্যক্ত জীবনবাদ আমাদের সাংস্কৃতিক অনন্যতা ও বিশিষ্ট জীবনচেতনার সাক্ষ্য।
তারপরেও কী আমরা থেমেছি! রামমোহনের ব্রাহ্মমত, বিদ্যাসাগরের শ্ৰেয়োবোধ, ওহাবী ফরায়েজী মতবাদ, রবীন্দ্রনাথের মানবতা, নজরুল ইসলামের মানববাদ কী সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমাদের এগিয়ে দেয়নি?
মনীষা ও দর্শনের জগতে বাঙালি মীননাথ, কানপা, তিলপা, শীলভদ্র, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ, জীমূতবাহন, রঘুনাথ, রঘুনন্দন, রামনাথ,চৈতন্যদেব, রূপ-সনাতন-জীব-রঘুনাথাদি গোস্বামী, সৈয়দ সুলতান, আলাউল, হাজী মুহম্মদ, আলিরজা, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, কৃত্তিবাস-কাশীদাস রামমোহন-বিদ্যাসাগর-মধুসূদন, তীতুমীর-শরীয়তুল্লাহ্-দুদুমিয়া, বঙ্কিম-রবীন্দ্র-প্রমথ-নজরুল নির্মাণ করেছেন বাঙালি মনীষার ও সংস্কৃতির গৌরব মিনার। এঁদের কেউ বলেছেন ঘরের ও ঘাটের কথা, কেউ জানিয়েছেন জগৎ ও জীবন-রহস্য; কারো মুখে শুনেছি প্রেম, সাম্য ও করুণার বাণী; কারো কাছে পেয়েছি মুক্তবুদ্ধি ও উদারতায় দীক্ষা; কেউবা শিখিয়েছেন ঘর বাঁধা ও ঘর রাখার কৌশল, কেউ শুনিয়েছেন ভোগের বাণী, কেউ জানিয়েছেন ত্যাগের মহিমা, আবার কেউ দেখিয়েছেন মধ্যপন্থার ঔজ্জ্বল্য। আত্মিক, আর্থিক, সামাজিক, পারমার্থিক সব চিন্তা, সব মন্ত্রই আমরা নানাভাবে পেয়েছি এদের কাছে।
বাঙালির বীর্য হানাহানির জন্যে নয়, তার প্রয়াস ও লক্ষ্য নিজের মতো করে স্বচ্ছন্দে বেঁচে থাকার। স্বকীয় বোধ-বুদ্ধির প্রয়োগে তত্ত্ব ও তথ্যকে, প্রতিবেশ ও পরিস্থিতিকে নিজের জীবনের ও জীবিকার অনুকূল ও উপযোগী করে গড়ে তোলার সাধনাতেই বাঙালি চিরকাল নিষ্ঠ ও নিরত। এই জন্যেই রাজনীতির তত্ত্বের (Theory) দিকটিই তাকে আকৃষ্ট করেছে বেশি–বাস্তব-প্রয়োজনে সে অবহেলাপরায়ণ; কেননা তাতে বাহুবল, ক্রুরতা ও হিংস্রতা প্রয়োজন। এজন্যেই কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ বাঙালির মানস-সন্তান হলেও নেতৃত্ব থাকেনি বাঙালির। বিদেশাগত ভূঁইয়াদের নেতৃত্বে সুদীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছর ধরে মুঘল বাহিনীর সঙ্গে সংগ্রামে জানমাল উৎসর্গ করতে বাঙালিরা দ্বিধা করেনি বটে, কিন্তু নিজেদের জন্যে স্বাধীনতা কিংবা সম্পদ কামনা করেনি। কিন্তু মননের ক্ষেত্রে সে অনন্য। নতুন কিছু করার আগ্রহ ও যোগ্যতা তার চিরকালের। প্রজারা যেদিন গোপালকে রাজা নির্বাচিত করেছিল, ইতিহাসের এলাকায় সেদিন ভারতের মাটিতে প্রথম গণতান্ত্রিক চিন্তার বীজ উপ্ত হল। সেদিন এ বিস্ময়কর পদ্ধতির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ কেবল বাঙালির পক্ষেই সম্ভব ছিল।
ওহাবী, ফরায়েজী ও সশস্ত্র বিপ্লবকালে বাঙালির বল ও বীর্য, ত্যাগ ও অধ্যবসায় বাঙালির গৌরবের বিষয়।
স্বাতন্ত্র আসে উৎকর্ষে, অনন্যতায় ও অনুপমতায়–বৈপরীত্যে ও বিভিন্নতায় নয়। বাঙালির সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্রও তার উৎকর্ষে, নতুনত্বে ও অনন্যতায়। আমাদের দুর্ভাগ্য ও লজ্জার কথা এই যে, ইংরেজ আমলে ইংরেজি শিক্ষিত অধিকাংশ বাঙালি লেখাপড়া করে কেবল হিন্দু হয়েছে কিংবা মুসলমান হয়েছে, বাঙালি হতে চায়নি। হিন্দুরা ছিল আর্য-গৌরবের ও রাজপুত-মারাঠা বীর্যের মহিমায় মুগ্ধ ও তৃপ্ত এবং মুসলমান ছিল দূর অতীতের আরব-ইরানের কৃতিত্ব-স্বপ্নে বিভোর। এরা স্বাদেশিক স্বাজাত্য ভুলেছিল, বিদেশীর জ্ঞাতিত্ব গৌরবে ছিল তৃপ্তমন্য। এদের কেউ স্বস্থ ও সুস্থ ছিল না। তাই বাঙলা সাহিত্যে আমরা কেবল হিন্দু কিংবা মুসলমানই দেখেছি। বাঙালি দেখেছি ক্কচিৎ। এজন্যেই আমাদের সংস্কৃতি আশানুরূপ বিস্তার ও বিকাশ পায়নি। আজ বাঙালি পায়ের তলার মাটির সন্ধান নিচ্ছে। এই মাটিকে সে আপনার করে নিচ্ছে। এর মানুষকে ভাই বলে জেনেছে। আজ আর কেবল ধর্মীয় পরিচয়ে সে চলে না। স্বদেশের ও স্বভাষার নামে পরিচিত হতে সে উৎসুক। দুর্যোগের তমসা অপগতপ্রায় প্রভাত হতে দেরী নেই সামনে নতুন দিন, নতুন জীবন। নিজেকে যে চেনে, অন্যকে জানা-বোঝা তার পক্ষে সহজ। আজ বাঙালি আত্মস্থ হয়েছে। তার আত্ম-জিজ্ঞাসা য়েছে প্রখর, সংহতি কামনা হয়েছে প্রবল। শিক্ষিত তরুণ বাঙালি জেগেছে, তাই সে তার ঘরের লোককে জাগাবার ব্রত গ্রহণ করেছে। বলছে বাঙালি জাগো। জাগ্রত মানুষই সংস্কৃতি চর্চা করে। এবার স্বস্থ ও প্রকৃতিস্থ বাঙালি জাগবে ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে দ্রুত এগিয়ে যাবে। জীবনে ও জগতে সে নতুনকে করবে আবাহন এবং নতুন ও ঋদ্ধ চেতনায় হবে প্রতিষ্ঠিত।
ভাষা প্রসঙ্গে : বিতর্কের অন্তরালে
০১.
পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই ভাষার প্রশ্নটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। শিক্ষায় ও সম্পদে অগ্রসর সাবেক যুক্তপ্রদেশের নেতারা ও পদস্থ কর্মচারীরা এবং পাঞ্জাবের মুসলমান জমিদাররা ও পদস্থ চাকুরাই পাকিস্তানে প্রশাসনিক কর্তৃত্ব লাভ করে। এদের ভাষা ছিল উর্দু। পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো আঞ্চলিক বুলিই তখনো লেখ্য ভাষা হিসেবে প্রয়োজনানুরূপ বিকাশ পায়নি। তার উপর পাকিস্তানভুক্ত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জনসমাজে তখনো অশিক্ষার অন্ধকার বিদ্যমান।
উর্দুভাষী শাসক-প্রশাসকেরা যখন কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের সুযোগে তাদের মাতৃভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে কৃতসংকল্প, তখন প্রায়-বুলি-নির্ভর পশ্চিম পাকিস্তানীদের আপত্তির কোনো কারণ ঘটেনি। তাছাড়া নতুন রাষ্ট্রপ্রাপ্তির উল্লাস এবং বিজাতি বিদ্বেষজাত ইসলামী বেরাদরী ভাবটাও ছিল তখন জনমনে প্রবল। পূর্ব-বাঙলার একশ্রেণীর শিক্ষিত লোকেরও ছিল এই বেরাদরী উদারতা ও হিন্দুভীতি। তারাও হিন্দুস্তানী ও পাঞ্জাবী বেরাদরের প্রতি সর্বব্যাপারে ছিল শ্রদ্ধাবান ও নির্ভরশীল। তার উপর, জিন্নাহর কায়েদে আযম নামের ফাঁকে একটা personality cult বা ব্যক্তিপূজার প্রবণতা জনসমাজে গভীর ও ব্যাপক রূপ নিয়েছিল। উর্দুভাষী অনুচরদের প্রভাবে গুজরাটী-ভাষী জিন্নাহও উর্দুর পক্ষে রায় দিলেন। কাজেই অনুগ্রহজীবী বাঙালি নেতারাও এদের কেউ কেউ ছিলেন উর্দুভাষী] জুটে গেলেন উর্দুর দলে। বাকি রইল বাঙলার ছাত্র, সাহিত্যিক ও তরুণ বুদ্ধিজীবীরা। ছাত্রদের সক্রিয় সংগ্রামে অবশেষে বাঙলা মৌখিক স্বীকৃতি পেল, কিন্তু অকপট অন্তরে গৃহীত হল না অবাঙালি সমাজে। তার গূঢ় কারণ ছিল।
.
০২.
মাতৃভাষার প্রতি নিছক প্রীতিবশেই তারা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করতে চায়নি, চেয়েছিল সাম্রাজ্যিক স্বার্থলোভে। কেননা তারা জানত স্বাধর্মের নামে বিধর্মী-বিদ্বেষ জাগিয়ে সাময়িক সাফল্য অর্জন সম্ভব হলেও বৈষয়িক ব্যাপারে এ কখনো স্থায়ী প্রেরণার আকর হতে পারে না। কাজেই বিধর্মী বিদ্বেষপুষ্ট ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবোধের উত্তেজনা দুই বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে সাময়িক সংহতি দান করলেও তা নিতান্ত নশ্বর। অতএব পরিণাম ভেবেই তারা সাম্রাজ্যবাদীর সাম্রাজ্যিক নীতি গ্রহণ করে শোষণের স্থায়ী ব্যবস্থা রাখার উদ্দেশ্যেই। ইতিহাস বলে এবং সবাই জানে, কেবল বাহুবলে শাসন শোষণ কায়েম রাখা চলে না। শাসিত জনকে অনুরক্ত করেই আনুগত্য আদায় করতে হয়। এর পরীক্ষিত ও অমোঘ ফলপ্রসূ উত্তম উপায় হচ্ছে, নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে শাসিত জনের মনে-মেজাজে একপ্রকার মুগ্ধতার কুয়াশা রচনা করা। শাসকজাতির ভাষার মাধ্যমে তাদের সাহিত্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, দর্শন ও ইতিহাস শাসিত জনের মনে মাকড়সার জাল তৈরি করে, তার ফলে শাসকগোষ্ঠীর প্রতি শাসিতজন শ্রদ্ধাবান ও সহিষ্ণু হয়ে উঠে। ধনের, মানের ও মর্যাদার ক্ষেত্রে শাসিতজনের হীনমন্যতা এবং শাসকগোষ্ঠীর উত্তমন্যতাও এ ক্ষেত্রে আনুকূল্য করে। চিরকাল এমনি উদ্দেশ্যে বিদেশী শাসকরা শাসিতজনের মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে বা তার বিকাশ রুদ্ধ করে নিজেদের ভাষা ও বর্ণমালা চালু করেছে। এর ফলে শাসিতজনের বুদ্ধি হয় আড়ষ্ট, চিন্তাশক্তি পায় হ্রাস, দৃষ্টি হয় আচ্ছন্ন, মন থাকে অনুরক্ত। এমনি অবস্থায় আনুগত্যের স্বস্তিই হয় প্রজার কাম্য। প্রতীচ্যবিদ্যার ও সংস্কৃতির প্রভাবে এদেশের শিক্ষিত সাধারণেও ব্রিটিশ-প্রীতি এমনি গাঢ় হয়ে উঠেছিল বলেই সিপাহী-বিপ্লব কালে তা যে শুধু নিষ্ক্রিয় ছিল তা নয়, ইংরেজদের বিপর্যয়ে উদ্বিগ্নও হয়েছিল এবং ব্রিটিশ-বিজয়ে তাদের উল্লাসের সীমা ছিল না। অতএব শাসিত-মনে জরা ও জীর্ণতা দানের মোক্ষম উপায় হচ্ছে তাদের ভাষা কেড়ে নেয়া এবং শাসকগোষ্ঠীর ভাষা চালু করা।
.
০৩.
গোড়া থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানীরা অবচেতনভাবেই উপলব্ধি করেছিল পূর্ব বাঙলা হবে তাদের খাজনা উসুলের জমিদারী এবং শুল্ক আদায়ের বন্দর–একটি অনায়াসলব্ধ উপনিবেশ। ভেততা ও ভীতু বাঙালি নেতাদের প্রাণী বিশেষের মতো আনুগত্য তাদের লোভ ও ঔদ্ধত্য বাড়িয়ে দিয়েছিল। তারা লক্ষ্য করেছিল, বাঙালিরা তখন বেরাদরীভাবে বিগলিত। সামরিক ও বেসামরিক চাকরির ব্যাপারে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কিংবা আঞ্চলিক উন্নয়ন প্রকল্পে তাদের ন্যায্য দাবি উত্থাপনে তারা পরম উদারতায় উদাসীন। এই ঔদাসীন্য যেন চিরস্থায়ী হয়, তার জন্যে তারা নানা ছলাকলা উদ্ভাবনে সদাতৎপর। এর মধ্যে একটি হচ্ছে ইসলাম। দেশে অমুসলমান প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, তবু বাঙালির স্থায়ী আনুগত্য লাভের দুরাশা বশে তারা বাঙালির মনে ইসলামী উত্তেজনা জাগিয়ে রেখে, তাদের মনে বিধর্মী-বিদ্বেষকে তথা হিন্দু-ফোবিয়ায় স্থায়িত্ব দানে প্রয়াসী, তার আনুষঙ্গিক উপসর্গ হচ্ছে মুসলিম তমদুনের ধুয়া। আর তমদুন রক্ষার জন্যে প্রয়োজন ইসলামী সাহিত্য এবং তা মিলবে উর্দুভাষায় ও সাহিত্যে এবং আরবি ফরাসি শব্দে। আবার এই উর্দুভাষা ও আরবি-ফরাসি শব্দ অনায়াস আয়ত্তে পেতে হলে উর্দু হরফে (বিকল্পে রোমান হরফে) বাঙলা লেখা প্রয়োজন।
এ সহজ সদ্বুদ্ধি যদি কুফরী মন না-ই গ্রহণ করে, তবে অন্তত কিছু হরফ বর্জন করে, বানান সরল করে বাঙলা ভাষাকে বিকৃত কর, যাতে তা পৃথক রূপ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গীয় কাফের-প্রভাব থেকে মুক্ত হয়। অতএব, উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার অভিপ্রায়, এবং সে-প্রয়াসে ব্যর্থ হয়ে হরফ বদলানো, বানান পাল্টানো, আরবি-ফারসি শব্দ বসানো প্রভৃতির অভিসন্ধি মূলত এই ষড়যন্ত্রে সিদ্ধি-লক্ষ্যে প্রযুক্ত। পোষা হাতি দিয়ে বুনো হাতি বাধার মতো এসব অপকর্মে যারা নিয়োজিত, তারা আমাদেরই পরিজন। এজন্যে ষড়যন্ত্রের স্বরূপ সরল সাধারণ বাঙালির কাছে স্পষ্ট নয়। তাই তারা বিভ্রান্ত ও প্রতারিত।
.
০৪.
বাঙালি-মনে জড়তা ও জীর্ণতা দানের গোপন উদ্দেশ্যে তারা যেসব পন্থা উদ্ভাবন করেছে এবং জাতীয় জীবন বিকাশে সেসবের উপযোগ ও ফলপ্রসূতা প্রমাণের জন্যে তারা সাধারণত যেসব যুক্তি উপস্থাপিত করে, আমাদের মন্তব্য-সমেত সেগুলো এখানে তুলে ধরছি :
১. তারা বলে বাঙলা আরবি-ফারসি শব্দ-বহুল ছিল। উনিশ শতকে পাদরী ও পণ্ডিতের ষড়যন্ত্রে বাঙলা সংস্কৃতি-ঘেঁষা হয়ে উঠেছে। এর মূলে কোনো সত্য নেই। পনেরো শতকের শাহ মুহম্মদ সগীর থেকে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কবি চুহর অবধি কবির লিখিত রচনায় এবং গোপীচাঁদ-ময়নামতীর গান, পূর্ববঙ্গ-ময়মনসিংহগীতিকা, বাউলগান থেকে অল্পশিক্ষিত আজকের কবির মৌখিক রচনা অবধি কোথাও আরবি-ফরাসি শব্দবহুল বাঙলার নমুনা মেলে না।
হাওড়া-হুগলী-কোলকাতা-মুর্শিদাবাদ অঞ্চল ছিল আন্তর্জাতিক ও আন্তরাঞ্চলিক বাণিজ্যকেন্দ্র। য়ুরোপীয়রা ছাড়াও ভারতের, ইরানের ও মধ্য-এশিয়ার লোক এখানে বাস করত। ফারসি ও হিন্দি ছিল Lingua Franca ভাব বিনিময়ের ভাষা। স্থানীয় বাঙলার সঙ্গে ফারসি-হিন্দির মিশ্রণে গড়ে উঠে খিচুড়ি বাঙলা। এর উদ্ভব ও প্রকৃতি অবিকল দাখিনী উর্দু ও উত্তর ভারতীয় উর্দুর মতোই। এটি ছিল বন্দর এলাকার সঙ্কর বাঙালির বুলি। উক্ত অঞ্চলের বাইরে এর কোনো প্রভাব পড়েনি। সত্যপীর পাঁচালী প্রণেতা এই অঞ্চলের হিন্দু কবিরা সুলতান সৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহর বংশোদ্ভব বলে কথিত সত্যপীরের মুখে বিকৃত হিন্দুস্থানী বুলি প্রয়োগ শুরু করেন সতেরো শতক থেকেই। এঁদের অনুকরণে ১৭৬০ সনের পরেরকার কবি হুগলী বন্দরের শায়ের ফকির গরীবুল্লাহ বাঙলা ও হিন্দুস্থানী বাক্রীতির মিশ্রণে কাব্যরচনা করেন। তাকে অনুসরণ করেন হাওড়াবাসী কবি সৈয়দ হামজা। উনিশ ও বিশ শতকে এ অঞ্চলের মালে মুহম্মদ, জনাব আলী, রেজাউল্লাহ, মুহম্মদ খাতের, মুহম্মদ দানিশ, আবদুল মজিদ প্রভৃতি প্রায় শত পেশাদার শায়ের উক্ত মিশ্ররীতি প্রয়োগে অনুবাদমূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন।
উনিশ শতকের শেষার্ধে মীর মশাররফ হোসেন, রিয়াজ আল দীন, মাশহাদী প্রমুখ মুসলিম লিখিয়েরা এর নাম দেন দোভাষী রীতি। বিশ শতকে হিন্দুরা এর নাম রাখেন মুসলমানী বাঙলা। আর ১৯৪০ সনের পরে মুসলমানরা এ সাহিত্যের নাম দেন পুথি-সাহিত্য। কোলকাতার ছাপাখানার বদৌলতে এগুলো সারা বাঙলা দেশে প্রচার লাভ করে। বিকল্প পাঠ্যগ্রন্থের অভাবে গ্রাম-বাঙলার স্বল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত মুসলমান শোধ্ব বছর ধরে এগুলো পড়েছে–শুনেছে বটে, কিন্তু এর বাীতি বা ভাষার দ্বারা কোথাও কেউ কখনো প্রভাবিত হয়নি। প্রমাণ পুথিসাহিত্য পড়য়া গ্রাম্য বাঙালির রচিত গান-গাথা, কবিতা এবং কথাবার্তা।
পূর্বোক্ত অঞ্চলে ছাড়া অন্যত্র বাঙলা ভাষায় যে আরবি-ফারসি শব্দ বিরল ছিল, তা কেবল হালহেড় বা ফরস্টারের উক্তি থেকেই নয়, কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ কিংবা ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সম্বাদ-এর ভাষা থেকেও প্রমাণিত। উক্ত বন্দর ও শাসন-কেন্দ্রের সঙ্কর বাঙালিরা ছাড়াও দরবারীভাষা ফারসি শিক্ষিত অসাহিত্যিক বাঙালিরা কথাবার্তায় ও বৈষয়িক চিঠিপত্রে, দলিল দস্তাবেজে দেদার ফারসি শব্দ ব্যবহার করত, এখনকার অসাহিত্যিক রচনায় কিংবা কথাবাতায় ইংরেজি শিক্ষিত লোকেরা যেমন অজস্র ইংরেজি শব্দ প্রয়োগ করে। তাই বলে গ্রাম-বাঙলার অশিক্ষিত মানুষকে পূর্বে ফারসি এবং এ যুগে ইংরেজি ভাষা প্রভাবিত করেছে বললে সত্যের অপলাপই হয়। প্রমাণস্বরূপ বলা চলে বাঙলার পল্লী অঞ্চলের মুসলমান নারী-পুরুষদের যারা পুরুষানুক্রমে চিরকাল নিরক্ষর, তাদের উপর নিশ্চয়ই উনিশ শতকের পাদরী ও পণ্ডিতের কিংবা এ যুগের পুস্তকী ভাষার প্রভাব পড়ার উপায় ছিল না বা নেই। তবে তাদের আঞ্চলিক বুলিতে শাস্ত্রীয় কিংবা সরকার সম্বন্ধীয় পরিভাষা ব্যতীত অন্য আরবি-ফারসি-হিন্দির প্রভাব নেই কেন!
২. তারা আরবি-ফারসি শব্দের মধ্যেই ইসলাম ও তমদুনের স্থিতি প্রত্যক্ষ করে। অথচ এ দুটোই ইসলাম-পূর্ব যুগের পৌত্তলিক-বেদীনের ভাষা। তবু আল্লাহ ও ইলাহী শব্দদুটোকে নতুন তাৎপর্যে গ্রহণ করতে অসুবিধে হয়নি। সাকার সকন্যা দেবতা মুহূর্তে নিরবয়ব স্রষ্টার ভাবরূপ লাভ করেছেন মুসলিম মনে, এমনকি ইসলামী অঙ্গীকারের মৌল শব্দগুলো–আল্লাহ, রসুল, মক, জান্নাত, জাহান্নাম, সালাত, সিয়াম প্রভৃতি ইরানে খোদা, পয়গম্বর, ফেরেস্তা, বেহেস্ত, দোজখ, নামায, রোযা রূপে অনূদিত ও গৃহীত হয়েছে। পাক-ভারতে ইরানী পরিভাষাই গৃহীত হয়েছে, তৎসঙ্গে খোদার দেশী পরিভাষাও যুক্ত হয়েছিল : নিরঞ্জন, নাথ, ধর্ম, করতার এবং বেহেস্ত দোজখও হয়েছিল স্বর্গ ও নরক।
উল্লেখ্য যে একটি আরবি শব্দও সরাসরি পাক-ভারতের ভাষায় গৃহীত হয়নি। সব কয়টিই এসেছে ফারসির মাধ্যমে। আর উর্দু বলে কোনো ভাষা ছিল না বা নেই। বৈদিক ভাষার উত্তরভারতীয় আঞ্চলিক বুলিতে ফারসি শব্দের আধিক্যে ও ফারসি হরফ প্রযুক্ত হয়ে গড়ে উঠেছে আধুনিক উর্দু। উর্দু নামটাই অর্বাচীন। এটি একটি মঙ্গোলীয় শব্দ, অর্থ সৈন্য-শিবির। সামরিক বাহিনীর তথা সৈন্য-শিবিরের Lingua Franca অর্থে চালু হল এটি।
বিদেশাগত শাসক-প্রশাসক ও তাদের অনুচরেরা প্রয়োজনানুরূপ দেশী শব্দ আয়ত্ত করার অসামর্থবশে উত্তরভারতীয় ভাষায় তুর্কী-ফারসি শব্দের বহুল প্রয়োগে ভাব প্রকাশ করত এবং দেশী হরফ শিক্ষার ঝামেলা এড়িয়ে ফারসি হরফে পরবর্তীকালে লেখাও শুরু করল। এভাবে ফারসি শব্দবহুল এবং ফারসি হরফে লিখিত একটি ভাষা দাঁড়িয়ে গেল। তবু জাতি বিচারে উর্দু একটি আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষা। কেননা শব্দ দিয়ে ভাষার জাতি নির্মিত হয় না, হয় বাক্য-গঠন রীতি বা ব্যাকরণ দিয়ে। তাছাড়া শব্দের দিক দিয়ে পৃথিবীর যাবতীয় ভাষাই–সভ্যজাতির ভাষা মাত্রই মিশ্র। অবশ্য ফারসিও যে বৈদিকি ভাষার জ্ঞাতি-পহ্লবী ভাষার আধুনিক রূপ, তাও এ সূত্রে স্মর্তব্য। প্রমাণস্বরূপ বলা চলে ষোলো শতকের উত্তরভারতীয় কবি কুতবন, মালিক মুহম্মদ জায়সী, মিয়া সাধন, এয়ারী, কবীর, দাদু, রজব, দরিয়া প্রমুখ সবাই আঞ্চলিক হিন্দিতে নাগরী হরফেই কাব্য রচনা করেছেন, তখনো ঐ রিখতার ভাষা ছিল হিন্দবী (আমীর খুসরু) দাখানী (দাক্ষিণাত্যে) দেহলবী (আবুল ফজল), হিন্দি বা গুজারী বা গুজরাটী (গুজরাটে)। শিবিরের ভাষা হিসেবে উর্দু নাম সতেরো শতকের শেষের দিকে সৈন্য-সমাজে হয়তো চালু হয়েছিল।
আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে উর্দু নাম সাধারণ্যে চালু হতে থাকলেও উনিশ শতকের আগে এ নাম সর্বজনগ্রাহ্য বা তেমন জনপ্রিয় হয়ে উঠেনি। আঠারো শতকেও উর্দু গদ্য হিন্দি নামে এবং উর্দু কবিতা রিখতা নামে পরিচিত ছিল। স্যার সৈয়দ আহমদের পত্ৰসূত্রে জানতে পাই উনিশ শতকের শেষার্ধেও দিল্লী থেকে বিহার অবধি অঞ্চলের ভাষার নাম ও হরফ নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে দ্বন্দ্ব-বিরোধ ছিল। হিন্দুরা ছিল হিন্দি-নামের ও নাগরী হরফের পক্ষপাতী আর মুসলমানেরা ছিল উর্দু নামের ও ফারসি হরফের অনুরক্ত। আরো দুটো তথ্য স্মর্তব্য : ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের জন গিলাইস্টের প্রবর্তনাতেই উর্দুভাষা স্বাতন্ত্র্য লাভের সৌভাগ্য অর্জন করেছে এবং এ ভাষা মুসলিম রাজশক্তির ও সংস্কৃতির পতন যুগেই বিকাশ লাভ করে। অতএব, এটি উজ্জীবিতের নয়, নির্জিতের ভাষা ও সাহিত্য। এ কারণেই সম্ভবত প্রখ্যাত মুসলিম কবিদের শ্রেষ্ঠ রচনার বাহন হয়েছে ফারসি-উর্দু নয়।
৩. এদের আর একটি যুক্তি : উর্দুভাষা ইসলামী শাস্ত্র, সাহিত্য ও তমদুনের আকর।
ভাষার গুণেই কী ধর্মীয় শাস্ত্র, সাহিত্য ও তমদুন গড়ে উঠে? ধর্মভাব থাকে মনে, তা-ই প্রকাশিত হয় ভাষায় ও আচরণে। মুসলমানের অভিপ্রায় ও প্রচেষ্টাতেই আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় ইসলামী শাস্ত্রগ্রন্থ রচিত হয়েছে। অমুসলমানের আগ্রহে যেমন ইংরেজি, ফরাসি ও জার্মান ভাষায় রচিত হয়েছে ইসলাম ও মুসলিম সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাস সম্পর্কিত নানা গ্রন্থ। বাঙলায় যে শাস্ত্রগ্রন্থ নেই–এ-তথ্যই বা তারা সংগ্রহ করল কিরূপে? আর যদি না-ই থাকে, তাহলে প্রয়োজনবোধে বাঙলায় ইসলামী শাস্ত্র, সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শন গ্রন্থ রচনা করতে ভাষাগত কিংবা স্থানগত বাধা আছে কি?
মানুষের মনের যে ভাব-ভাবনা জেগে উঠে, তা-ই তার ভাষায় লিখিত বা রচিত রূপে প্রকাশ পায়। বাঙালি যদি ইসলাম চর্চায় মনোযোগী হয়, সে প্রয়োজন অনুভব করে, তাহলে অন্যান্য বিষয়ে যেমন সে গ্রন্থ রচনায় সমর্থ, এ বিষয়েও সে কাজ করবে, বই লিখবে, বাইরের লোকের এ ব্যাপারে মুরুব্বিয়ানা অহেতুক। কেননা বাঙালি মুসলমানরা হাজার বছরের পুরোনো মুসলমানের বংশধর। ইসলামের কী তার অজানা রয়েছে যে, সে রাজনৈতিক কারণে নতুন পীরের মুরিদ হবে? তাছাড়া নিছক ধর্মীয় কোনো তমদুন থাকতে পারে না। তাই যদি হত, তাহলে ভূগোল ও কাল নিরপেক্ষ একটি নিবর্ণ ও চিরন্তন বিশ্বমুসলিম সংস্কৃতি থাকত। দেশান্তরে ও কালান্তরে তা রূপান্তর লাভ করত না। বস্তুত দেশ-কাল-ব্যক্তি নিরপেক্ষ এবং শৈক্ষিক, আর্থিক, সামাজিক ও নৈতিক প্রতিবেশবিরহী কোনো সংস্কৃতি কল্পানাতীত। সংস্কৃতি তাই স্বরূপত ব্যক্তিক ও অবস্থানিক বা পারিবেশিক। ইসলামে অনুরাগই যদি উর্দুপ্রীতির কারণ হয়ে থাকে, তাহলে আরবিকেই আমাদের রাষ্ট্রভাষা করা উচিত। স্মর্তব্য যে আরবি-ফারসি কিংবা উর্দুর সবটা শাস্ত্রীয়ও নয়, সু-মুসলমানের রচনাও নয়। আজো উক্ত তিন ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখকেরা সব মুসলিম নন। আজো আরবিভাষী লোকের শতকরা পনেরো জন খ্রীস্টান ও ইহুদী। উর্দুও কেবল মুসলমানের দানে ঋদ্ধ হয়নি। কাজেই আরবি-ফারসি শব্দ ও সাহিত্য মাত্রই ইসলামী নয়, একাধারে অমুসলিমেরও। অতএব বাঙলা ভাষার নিন্দা-কলঙ্ক রটানোর মূলে অভিসন্ধিই ক্রিয়াশীল। ন্যায়ত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাঙলাই হওয়া উচিত ছিল পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। বেরাদরীভাবে বিগলিত আত্ম-প্রত্যয়হীন হীনমন্য ও প্রভুগত প্রাণ বাঙালিরা সে-কথা ভাবতেও সাহস পায়নি। ফলে উত্তরভারতের ভাষা আপাতত আসন জুড়ে বসেছে পাকিস্তানে। এ অন্যায়েরও জবর-দখলের পক্ষে নৈতিক সমর্থন সঞ্চয়ের জন্যেই এত ছল-চাতুরীর আশ্রয় ও প্রশ্রয় জরুরি হয়েছে।
বলেছি, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকালে উর্দুকে অস্বীকার করবার মতো ভাষার ঐশ্বর্য ছিল না পশ্চিম পাকিস্তানীদের। আজ তারাও মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে। ইতিমধ্যে তাদের অনলস সাধনায় তারা স্ব স্ব ভাষাকে অনেকখানি উন্নত করেছে। কাজেই আত্মপ্রত্যয় নিয়ে কথা বলবার মতো নৈতিক ভিত্তিও রচিত হয়েছে তাদের। এর মধ্যেই সিন্ধি, সারাইকী, পশতু ও বেলুচ ভাষীরা ভাষার ক্ষেত্রে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে তারা আত্মসম্মানবোধে ও পরিণাম চিন্তায় বিচলিত। তাই তারা আজ প্রবুদ্ধ ও উচ্চকণ্ঠ। আজ যখন পাকিস্তান প্রাপ্তির উচ্ছ্বাস ও উল্লাস অপগত, আর স্ব-ভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে সবাই সচেতন এবং উর্দুও যখন রাষ্ট্রভাষা হিসেবে আজো স্বপ্রতিষ্ঠিত নয়, তখন পাকিস্তানে উর্দুর ভবিষ্যৎ নতুন করে যাচাই করার সময় এসেছে। রাষ্ট্রভাষা হিন্দির বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে যেমন, উর্দুর বিরুদ্ধেও তেমনি প্রতিবাদী দল অচিরেই পশ্চিম পাকিস্তানে গড়ে উঠবে–সে আশঙ্কা অমূলক নয়। ইতিমধ্যেই তার আভাস সুপ্রকট। পশ্চিম পাকিস্তানে পূর্বতন প্রদেশগুলোর পুনঃপ্রতিষ্ঠা এ আশঙ্কাকে প্রবল করছে। কেননা, প্রদেশগুলোর সংস্থিতি ভাষা-ভিত্তিক।
.
০৫.
বাঙলা ভাষার সংস্কার-প্ৰয়াস সরকারি-উদ্যোগেই শুরু হয়েছিল। শিশুরাষ্ট্র পাকিস্তানে তখন অনেক সমস্যা ছিল। বাঙলা ভাষার হরফ ও বানান কোনো সমস্যা ছিল না, তবু অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বাঙলা ভাষা সম্পর্কিত একটি কাল্পনিক সমস্যার সমাধান সরকারি অফিসে অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছিল। তারই ফলে ভাষা-সংস্কার কমিটিগুলো পর পর গড়ে উঠে–সরকারি কমিটি, বাঙলা একাডেমী কমিটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ও ব্যক্তিগত প্রয়াস চারদিক মাতিয়ে তোলে। ঐদিকে আরবি হরফে বাঙলা লেখানোর অভিযানও সরকারি অর্থে চলতে থাকে। প্রয়াসটা যে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রমূলক তা বুঝতে কারো বাকি থাকল না। উক্ত সব কমিটির সদস্যদের সবাই ভাষাবিদও ছিলেন না। সবচেয়ে বেদনাদায়ক ও ক্ষোভজনক আনাড়ির অনধিকার চর্চার আগ্রহ। অতএব কলকাঠি ঘুরাচ্ছিল যারা, তারা ছিল নেপথ্যে; পুতুল ও যন্ত্ররূপে যাদের সুমুখে দেখেছি, তাঁরা আমাদের ঘরের লোক–অনেকেই শ্রদ্ধেয়। তাই জনমনে প্রভাব পড়েছিল তাদের। এই কপট হিতৈষীরা তাই আজো নির্বিঘ্নে ভাষা সংস্কার রূপ মহাসমস্যা নিয়ে উদ্ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন। মাঝে মাঝে তারা দুঃস্বপ্নের মতো জেগে উঠেন। আতঙ্কিত করেন আমাদের। এর পশ্চাতে মূল উদ্দেশ্য বাঙলা ভাষাকে বাঙালির মতানৈক্যের সুযোগে রাষ্ট্রভাষার অধিকারচ্যুত করা। আর আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য রোমান হরফ বা আরবি হরফ চালু করে এর বিকৃতি সাধন করে বিকাশ-পথ রুদ্ধ করা এবং তৎসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বাঙলা ভাষার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া।
১. তাঁরা বলেন, শব্দের বানান উচ্চারণ অনুযায়ী হওয়া উচিত। প্রশ্ন জাগে, পূর্ব বাঙলার কোনো দুটো অঞ্চলের উচ্চারণ এরকরম নয়। ভাষাবিজ্ঞান বলে–কোনো দুটো মানুষই অবিকল একরকম উচ্চারণ করতে পারে না। এমনকি কোনো মানুষের পক্ষেই কোনো শব্দ একই রূপে দুবার উচ্চারণ করাও সম্ভব নয়। তাহলে তারা কোন অঞ্চলের কোন্ ব্যক্তির উচ্চারণ অনুযায়ী বানান-পদ্ধতি নির্মাণ করবেন? তাছাড়া, যেহেতু উচ্চারণ জনে-জনে, স্থানে স্থানে ও কালে কালে বদলায়, সেহেতু উচ্চারণের অনুগত করে বানান সংস্কার করতে হলে প্রায় প্রতিজনের জন্যে ও প্রতিস্থানে এবং প্রতি পঞ্চাশ বছরে বর্ণ ও বানান বদলাতে হবে। তাহলেই কেবল বিজ্ঞান সম্মত সংস্কার সম্ভব। দুনিয়ার কোথাও কখনো শব্দের বানান উচ্চারণ-অনুগ হয় না।
উপরোক্ত কারণে হতে পারে না বলেই হয় না। লেখ্য ভাষার মাধ্যমেই এক দেশের মানুষ পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সাহিত্যিক ও ঐতিহ্যিক জ্ঞাতিত্ব রক্ষা করে। কেননা আঞ্চলিক বুলি প্রতিমুহূর্তে রূপান্তর লাভ করছে ও দেশের মানুষকে পারস্পরিক আত্মীয়তা ঘুচিয়ে স্বাতন্ত্র্য দান করছে। সেই লেখ্য ভাষার জোর নিহিত থাকে তার দীর্ঘকালীন অপরিবর্তনীয়তায়। অতএব, লেখ্য ভাষা মাত্রেই কৃত্রিম। কাজেই সাধারণ অর্থে মাতৃভাষা বলতে যা বুঝায়, আসলে এ তা নয়। বুলির মতো এ শৈশবে লভ্য নয়। একজন বিদ্বান বলেছেন, মাতৃভূমি মানে যেমন মামার বাড়ি নয়, মাতৃভাষাও তেমনি মায়ের মুখের বুলি নয়। অন্যান্য বিদ্যার মতো লেখ্য ভাষাও একটি বিদ্যা এবং তা অনায়াসলভ্য নয়। অন্যান্য শাস্ত্রের মতো ভাষাও পরিশ্রম করে আয়ত্ত করতে হয়।
২. তাঁদের আর একটি যুক্তি–কিছু বর্ণ বর্জন করে বানান সংস্কার করলে, শিক্ষার্থীর পক্ষে ভাষা শেখা সহজ হবে। কিন্তু তাতেই কী বানান ভুলের খপ্পর থেকে বাঁচা যাবে? বাধাকে-বাঁধা, চোরকে–চুর, বিধাতাকে–বিদাতা, বাড়িকে–বারি, ঘনিষ্ঠকে–ঘনিষ্ট, সম্বন্ধকে সম্মন্দ লেখার বিড়ম্বনা থেকে শিক্ষার্থীরা উদ্ধার পাবে কী করে? আসল কথা: শিখবার, জানবার, বুঝবার যোগ্যতা ও আগ্রহ যাদের থাকে তারাই কেবল ভাষা সমেত যে-কোনো বিদ্যা আয়ত্ত করতে পারে।
কেউ কেউ বলেন Type, Telegraph ও stenography-র জন্য বর্ণসংখ্যা কমানো দরকার। যন্ত্র তো আমাদের প্রয়োজনেই তৈরি। যন্ত্রকে আমরা আমাদের অনুগত করে নেব, আমরা কেন যন্ত্রের অনুগত হব? আরবি-উর্দু হরফের রয়েছে শব্দের আদ্যে-মধ্যে-অন্ত্যে তিনটি ভিন্ন রূপ। ইংরেজিরও Capital ও small letter যেমন রয়েছে, তেমনি হস্তাক্ষর পায় একেবারে ভিন্ন। অবয়ব। তাছাড়া ইংরেজির কয়েকটি বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি বিভিন্ন উচ্চারণে ব্যবহৃত হয়। যেমন, C ক, চ, Th—ত,দ, ghফ,উহ্য,ch–চ, ক, ou-আ, E–আ, এ, ই, a–এ্যা, আ, ই, আই, ইত্যাদি। এছাড়াও বর্ণের উচ্চারণ উহ্য তো থাকেই। কোনো ইংরেজি শব্দের উচ্চারণ বানান অনুগ নয়। তবু আমরাই এ বিদেশী ভাষার প্রত্যেকটি বানান নির্ভুলভাবে আয়ত্ত করেছি! বাঙলা বর্ণমালা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সাজানো, প্রত্যেকটা বর্ণ উচ্চারণসাধ্য। কেবল জ+ঞ=জ্ঞ ব্যতীত আর কোথাও বানানে ও উচ্চারণে অসঙ্গতি নেই। আধুনিক মুদ্রণালয়ে যুক্তবর্ণের অবয়ব সংস্কারের ফলে ব্যঞ্জন বর্ণগুলো প্রায় সর্বত্রই অবিকৃত ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কেবল স্বরবর্ণের কার ও কয়েকটি ব্যঞ্জনবর্ণের ফলা-ই যা ব্যতিক্রম।
৩. তাঁদের কাছে, ত-২, ই-ঈ, উ-ঊ, ঋ-র, ন-ণ, জ-য, খ-ক্ষ, ঙ-ং, ব-ভ মহাসমস্যার বিষয়। অথচ সব ভাষাতেই এমনি আপাত ঐক্যের পৃথক বর্ণ রয়েছে। ইংরেজিতে g-j-z, c-k, a-u-e, j-s, F-gh, x-ks, ct, cz ইত্যাদি এবং আরবিতে রয়েছে জিম-জাল-ডাল-জে-জোয়াই, কাফ কোয়াফ, হে-হামজা, আলিফ-আইন ইত্যাদি। তাছাড়া কৃত্রিম স্বর-চিহ্ন যুক্ত না হলে যে-কোনো স্বর যোগে আরবি, ফারসি, উর্দু শব্দের শুদ্ধ-প্রতিম বিকৃত উচ্চারণ সম্ভব।
৪. পাকিস্তানে সম্প্রতি চারটি ভাষা শিক্ষা আবশ্যিক। শাস্ত্রীয় ভাষা আরবি, সরকারি ভাষা ইংরেজি এবং রাষ্ট্রভাষা উর্দু ও বাঙলা। কেবল বাঙলা বানান সংস্কার করে কোনো লাভ হবে না, করতে হলে উক্ত চারটি ভাষারই উচ্চারণ-অনুগ বানান সংস্কার করতে হবে। তাহলেই আমাদের মহৎ জাতীয় উদ্দেশ্য সফল ও সার্থক হবে। অর্থাৎ উক্ত চার ভাষারই একটি করে পাকিস্তানীরূপ রচনা করতে হবে। তা কেবল পাকিস্তানীর হিতার্থে পাকিস্তানেই চলবে। যদি বিদেশী ভাষা বলে ইংরেজি, আরবি, উর্দু ভাষা সংস্কারে আমাদের অধিকার না থাকে, তাহলে বাঙলাতেও কী সে অধিকার থাকে? কেননা, পাকিস্তানের বাইরেও বাঙলা ভাষার মালিক আছে। অতএব, অপর তিনটে ভাষাই যখন যথাপূর্ব সকল জটিলতা ও অসঙ্গতি নিয়ে আমাদের শিক্ষার অঙ্গীভূত রয়েছে, তখন বেচারা বাঙলাকেও দয়া করতে বাধা কি?
৫. তাছাড়া, লেখ্য ভাষার প্রয়োজন কেবল শিক্ষার্থী ও শিক্ষিত লোকেরই। শিক্ষার্থীর শিক্ষা কেবল ভাষার উপর নির্ভর করে না। জটিলতর বিষয় ও বিদ্যা তাকে অর্জন করতে হয়। ভাষা বুঝলেই অঙ্ক কষা যায় না; কিংবা ইতিহাসে দর্শনে জ্ঞান অর্জিত হয় না। কিংবা দ্বিতীয় পাঠের . সুবোধ বালকের গল্পের ঋজু ভাষা দিয়ে দর্শন বা মনোবিজ্ঞান শেখা চলে না। অতএব ভাষার সারল্য ও জটিলতা বিষয়ানুসারী। যে বয়সে শিশু বর্ণশিক্ষা করে সে-বয়সে তার ধীশক্তি বিকশিত থাকে না। কাজেই তার শিক্ষা অনেকটা চোখ-কান নির্ভর ও স্মৃতিভিত্তিক। এজন্যে তার কাছে সরল জটিলের পার্থক্য সামান্য। তাই তাই তাই মামার বাড়ি যাই যেমন যুক্তাক্ষর বর্জিত, যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই-ও তেমনি। তাই বলে কী যে-কোনো অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকই কী শেষোক্ত চরণের তাৎপর্য বুঝবে? তার জন্যে বয়স ও বিদ্যার প্রয়োজন হয় না কি?
অতএব, অশিক্ষিত লোকের লেখ্য ভাষা নিয়ে কোনো সমস্যাই নেই। এবং সব শিক্ষিত লোকেরও ভাষার শুদ্ধাশুদ্ধ নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। তাদের বৈষয়িক জীবনে প্রযুক্ত ভাষায় বর্ণাশুদ্ধি কিংবা বাক্যাশুদ্ধি চিন্তায় বা কর্মে কোনো বিপর্যয় ঘটায় না। আর বানান শুদ্ধ হলেই যে ভাষাও বিশুদ্ধ এবং অর্থগ্রাহ্য হবে–তার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। ব্যাকরণ তথা শব্দের অভিধা, আসত্তি ও বাক-রীতি (syntax) আয়ত্তে না থাকলে ভাষা শুদ্ধরূপে বলা বা লেখা চলে না; আর ভাষা শুদ্ধ হলেই যে সুন্দর ও অভিপ্রেতভাব প্রকাশক হয় না, তার জন্যে যে বক্তার জ্ঞান, প্রজ্ঞা, রুচি, ভাব ও প্রকাশ-সামর্থ্য প্রয়োজন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।
অতএব, বিশুদ্ধ ভাষার প্রয়োজন শিক্ষকের, সাহিত্যিকের, চিন্তাবিদের ও পণ্ডিতের। তারাই নতুন ভাব-চিন্তা প্রকাশের জন্যে বিদেশী ভাব ও বস্তুর পরিভাষা সৃষ্টির জন্যে ভাষার অনুশীলন করেন। ভাষা তাদের পেশার ও নেশার অবলম্বন। তাই ভাষা তাদের সর্বক্ষণের সাথী এবং অস্ত্র ও শাস্ত্র। এঁদের জন্যেই ভাষার অবিকৃত রূপ রক্ষা করা প্রয়োজন। যাতে ধাতু ও শব্দমূলের সঙ্গে
তাদের পরিচয় ও সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ থাকে। কেননা প্রকাশের প্রয়োজনে তারা সর্বক্ষণ শব্দ খুঁজে বেড়ান। এবং প্রয়োজনবোধে তারা শব্দ সৃষ্টি করেন। এই সৃষ্টির উপকরণ হচ্ছে ধাতুমূল বা শব্দমূল। ওগুলো জানা না থাকলে নতুন শব্দ সৃষ্টি করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, পূর্ব বাঙলার সরকার, বাঙলা একাডেমী ও বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড ইংরেজি শব্দের বাঙলা পরিভাষা তৈরির জন্যে তামদুনিক প্রবণতাবশে আরবি ও ফারসির সাহায্য নিতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে বহুনিন্দিত সংস্কৃত ধাতু ও শব্দমূলকেই সম্বল করেছেন। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক : ক্ষা, ও সা–এ দুটোই ইচ্ছা বাঞ্ছব্যঞ্জক প্রকৃতি। এগুলো দিয়ে আকাঙ্ক্ষা, বুভুক্ষা, মুমুক্ষা, তিতিক্ষা কিংবা বুভুক্ষু, তিতিক্ষু প্রভৃতি বিভিন্ন অর্থজ্ঞাপক শব্দ তৈরি হয়েছে; তেমনি পিপাসা, জিজ্ঞাসা, জিঘাংসা, উপচিকীর্ষা, অপচিকীর্ষা, লিঙ্গ, বিবমিষা প্রভৃতি শব্দ নির্মাণ সম্ভব হয়ছে। এমনি করে উপসর্গ ও প্রত্যয় যোগে প্রয়োজনমতো অসংখ্য শব্দ রচিত হয়ে ভাষাকে ঋদ্ধ ও সর্বপ্রকার ভাব-চিন্তা-অনুভূতি প্রকাশের যোগ্য করেছে। এভাবেই শব্দগুলো বিভিন্ন তাৎপর্যে সূক্ষ্ম ভাব-প্রতিম ও প্রমূর্ত-অনুভব হয়ে উঠে। মানব-মনীষার বিমূর্ত জগৎ এমনি করে সমূর্ত হয়ে ধরা দেয় সাধারণের কাছে।
জীবন যেহেতু গভীরতর অর্থে অনুভবের সমষ্টিমাত্র এবং যেহেতু সে-অনুভূতি অনুভবযোগ্য হয়ে রূপ পায় ভাষায়, সেহেতু ভাষা জীবানুভূতির নামান্তর মাত্র। মানুষের মানসার্জিত যা-কিছু সম্পদ তা বলতে গেলে এই ভাষারই দান। কাজেই সে-ভাষা নিয়ে আনাড়ির আস্ফালন শুধু-যে ঔদ্ধত্য, তা নয়, মারাত্মকও বটে।
মিলন-ময়দানের সন্ধানে
আদিম অসহায় ও অকুশল মানুষের শিকারে ও শস্য উৎপাদনে যৌথ প্রয়াসের প্রয়োজন ছিল। জ্ঞাতিত্বের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল এই যৌথ জীবন। ঐক্য ও সম্প্রীতি রক্ষার জন্যে রক্ত সম্পর্কে আরোপিত হয় অশেষ নৈতিক, আত্মিক ও সামাজিক গুরুত্ব। তাই জ্ঞাতিত্ববোধই মানুষের প্রথম পবিত্র দায়িত্ব বলে স্বীকৃতি লাভ করে আদিম সমাজে। জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের অবচেতন গরজে গড়ে উঠা এই বোধ ক্রমে আজন্ম লালিত সংস্কারে ও বিশ্বাসে পরিণতি পায়। এভাবে গভীর প্রত্যয়ে শুরু হয় গোত্রীয় জীবন।
মানব সমাজের শৈশবে-বাল্যে এ গোত্ৰ-চেতনা ও গোত্রীয় জীবন অশেষ কল্যাণ এনেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। কেননা সেদিন যৌথ প্রয়াস ছাড়া মানুষের আত্মরক্ষা ও আত্মপোষণ সম্ভব হত না। তারপর অভিজ্ঞতা, জ্ঞান ও বুদ্ধির ক্রমবিকাশে মানুষ ধর্ম তথা অভিন্ন আচার ও মতাদর্শের ভিত্তিতে রচনা করেছে বৃহত্তর সমাজ। গোত্রীয় চেতনাকে অতিক্রম করে জীবনের সংকীর্ণ পরিসরকে তারা সম্ভাবনার বিস্তৃত প্রান্তরে উন্নীত করল বটে, কিন্তু চেতনার গতি ও প্রকৃতি রইল। অপরিবর্তিত। ফলে স্বাধর্ম ও নবপ্রত্যয়ের প্রাচীর দিয়ে মানুষে মানুষে ব্যবধান বাড়িয়ে দিল। আগে। যেমন স্বগোত্রীয় না হলেই শত্রু মনে করা হত, এক্ষেত্রেও স্বমতের না হলেই পর মনে করা স্বাভাবিক হয়ে রইল।
আদিতে মানুষের যৌথ প্রয়াস প্রয়োজনীয় ছিল প্রকৃতি ও পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্যে। বিভিন্ন আঞ্চলিক গোত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এখন যৌথ জীবনের প্রয়োজন হল প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রের কবল থেকে খাদ্য ও খাক তথা জমি ও জীবন, জল ও জন্তু, প্রাণ ও মাল রক্ষার গরজে।
এই আত্মধ্বংসী গোত্রীয় বিবাদ নিরসনের জন্যেই মতবাদ ও আদর্শভিত্তিক জীবন-ভাবনায় প্রবর্তনা পায় মানুষ। তার থেকেই আসে ধর্ম নামের জীবন-নীতি। এতে পরিবর্তন মাত্র এটুকু হল। যে ক্ষুদ্র গোত্রীয় দ্বন্দ্ব এখন গোত্র সমষ্টির সমবায়ে গঠিত বৃহৎ সাম্প্রদায়িক হানাহানির রূপ নিল। অতএব চারিদ্র্যে ও আদর্শে কোনো রূপান্তর কিংবা উন্নয়ন ঘটেনি।
অভিজ্ঞতা, প্রকৌশল, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বুদ্ধি ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে নব উদ্ভূত মানবিক সমস্যার সমাধানের জন্যে যে আনুপাতিক চিন্তা-ভাবনা, পরিহার-সামর্থ্য, গ্রহণশীলতা ও সৃজনপ্রবণতা থাকা আবশ্যিক ছিল; অদূরদর্শী মানুষে তা কখনো সুলভ ছিল না। জ্ঞানী-মনীষীরা স্বকালের সমস্যার আপাত সমাধান পেয়েই চিরকালের মানুষের জন্যে প্রশস্ত জীবন-পথ রচনার গৌরব-গর্ব ও সাফল্য-সুখ অর্জন করতে চেয়েছেন। তারা নিজেদের মতাদর্শকে চরম ও পরম বলে জেনেছেন এবং জনগণকেও সে-ধারণা দিয়ে বিভ্রান্ত ও বিমূঢ় করে রেখেছেন। এভাবে তাঁদের। অজ্ঞাতেই তারা মানুষের মন করেছেন আনুগত্যের দীক্ষায় নিষ্ক্রিয় এবং মননক্ষেত্র করেছেন অসীম ভরসা দানে বন্ধ্যা।– বৈষয়িক ও জাগতিক আর সব ব্যাপারে মানুষ জানে অতীতের চেয়ে বর্তমান অনেক উন্নত। হোমারের চাইতে শেক্সপীয়ার, ভিঞ্চির চাইতে পিকাসো, সেন্ট অগাস্টাইনের চাইতে টয়নবী, জুলিয়াস সিজারের চাইতে জর্জ ওয়াশিংটন, ইডিপাস থেকে ফাউস্ট যে অনেক অগ্রসর তা কেউ অস্বীকার করে না। কিন্তু আদ্যিকালের শাস্ত্রের চাইতে উন্নত নিয়ম-নীতি কোথাও কখনো আর কিছু যে হতে পারে, তারা বরং প্রাণ দেবে, তবু তা স্বীকার করবে না। এখানে তারা প্রত্যয়-সর্বস্ব, অন্ধ ও গোঁড়া। বৈষয়িক ব্যাপারে তারা শ্রেয়সকে সহজেই গ্রহণ করে, নতুন স্বাচ্ছন্দ্যকে বরণ করবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠে; কিন্তু মতের ক্ষেত্রে, মননের জগতে, পুরোনোই তাদের প্রিয়, প্রাচীনত্বেই তারা পরিতৃপ্ত, বিশ্বাসেই তাদের ভরসা।
ফলে মানুষের বৈষয়িক ও প্রকৌশলিক অগ্রগতির সঙ্গে তাদের মন-মানসের আনুপাতিক সমতা রক্ষিত হয়নি। এ অসামঞ্জস্যজাত অসঙ্গতিই হচ্ছে আজকের দিনের মানবিক সমস্যার উৎস। তাদের জৈব জীবন এগিয়ে চলেছে, মনোজীবন রয়েছে অবিচল। জাগতিক জীবনে তারা বরণ করেছে চলমানতাকেই, মানস-জীবনে কামনা করছে স্থিতিশীলতাকে।
ইতিমধ্যে মানুষে মানুষে পৃথিবী ভরে উঠেছে। ভূ-তে বসতি-বিরল ভুবন নেই আর। বৈজ্ঞানিক আবিক্রিয়ায় ও প্রাত্যহিক প্রয়োজন বৃদ্ধির ফলে খণ্ড জগৎ অখণ্ড অঞ্চলে হয়েছে পরিণত। ঘেঁষাঘেঁষির জীবনে রেষারেষি হয়েছে প্রবল। প্রভাবের ও প্রতাপের টানাপড়েন অপরিসর জীবনকে প্রতিমুহূর্তে করছে প্রকম্পিত ও আন্দোলিত। অথচ গোত্রজ সংহতি ও ধর্মজ ঐক্য-ভিত্তিক সমাজ চেতনা আজো জগদ্দল হয়ে চেপে রয়েছে মানুষের বুকে। এ চেতনা নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের মন ও মেজাজ। আজকের দিনে যখন অব্যাহত গোত্রীয় স্বাতন্ত্র কিংবা একক ধর্মীয়-সমাজ অসম্ভব, তখন পরকে আপন করে নেয়ার মানস-প্রস্তুতি না থাকলে নির্ঘ নির্বিঘ্ন জীবন কিংবা সমাজ অথবা রাষ্ট্র থাকবে কল্পনাতীত। স্বগোত্রের, স্বধর্মের, স্বমতের ও স্বদেশের নয় বলেই মানুষকে যদি পর ভাবি, শত্রু মনে করি কিংবা অনাত্মীয় করে রাখি; তাহলে আজকের দুনিয়ার মিশ্র সমাজে, এজমালি জমিতে ও বারোয়ারী রাষ্ট্রে কেউ সুখে-শান্তিতে বাস করতে পারবে না। পারছে না যে তা কে অস্বীকার করবে? আফ্রিকার গোত্রীয় কোন্দল, য়ুরোপের জাতি-বৈর, আমেকিার বর্ণবিদ্বেষ, ভারতের সাম্প্রদায়িক চেতনা, পৃথিবীব্যাপী পরমত অসহিষ্ণুতা, ধর্মদ্বেষণা ও বিদেশী-বিদ্বেষ আজ মর্তমানবের যন্ত্রণার গোড়ার কথা। এই মৌল সমস্যার সমাধান না হলে স্বস্তি-শান্তির কোনো আপাত প্রলেপে মানব মনের এ দুষ্ট ক্ষতের নিরাময় নেই। এই দেশ-জাত-বর্ণ- ধর্ম চেতনা থেকে মুক্তি-সমাধানের প্রথম ও প্রধান শর্ত। কিন্তু এ মুক্তি সহজসাধ্য নয়। দীর্ঘমেয়াদী প্রচেষ্টায় অবশ্য সাফল্য সম্ভব। এজন্যে উদার রাষ্ট্রাদর্শ প্রয়োজন।
ধর্ম মানুষ ছাড়বে না। তবু ধর্মবোধের পরিবর্তন সাধন সম্ভব এবং এই লক্ষ্যেই চিন্তাবিদের ও রাষ্ট্রনায়কের প্রয়াস নিয়োজিত হওয়া আবশ্যিক। জনগণকে বলতে হবে–ধর্ম হবে আত্মিক, তা থাকবে ব্যক্তির বুকে এবং মন্দিরে-মসজিদে-চৈত্য-গীর্জায় ও সিনাগোগে। বাইরে বৈষয়িক, ব্যবসায়িক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে তার উপযোগ কিংবা প্রয়োজন নেই। বলতে হবে-বর্ণ বা অবয়ব হচ্ছে আবহাওয়ার দান, প্রাকৃতিক প্রভাবের প্রসূন। তার জন্যে মানুষে মানুষে প্রভেদ থাকতে পারে না। মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব ও হীনতা বিচারের ভিত্তি হবে শিক্ষা-জ্ঞান-প্রজ্ঞা-মনীষা ও চরিত্র। চণ্ডালও হবে দ্বিজশ্রেষ্ঠ যদি থাকে গুণ, জ্ঞান ও চরিত্র। দেশ ভেদে মানুষ শত্রু কিংবা মিত্র হতে পারে না। রুচি ও মনের মিলেই মানুষ হয় আত্মীয়। মানুষে মানুষে প্রীতিই একমাত্র মিলনসূত্র। মনে মনে গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে গেলে বাইরের কোনো বাধাই টিকতে পারে না। স্বামী ও স্ত্রীর মতো আপন কে? দাম্পত্যে কী আমরা ঘরে ঘরে পরকে চিরকাল আপন করে নিচ্ছিনে? দেশ-ধর্ম-জাত বর্ণের বাধাকে অতিক্রম করে কত কত দাম্পত্য গড়ে উঠেছে। এর পরেও কী বলব, অভিন্ন গোত্র বর্ণ-দেশ-ধর্ম না হলে মানুষে মানুষে মিলন সম্ভব নয়? অভিন্ন স্বার্থে সহযোগিতা ও সহাবস্থান যে সম্ভব, তার বহু বহু প্রমাণ কী আমরা অহরহ চারদিকার পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ করছিনে? গোত্র-প্রীতি আর ভূগোল-চেতনাও আসলে একটা সংস্কার। এ সংস্কার দুমুচ্য-দুরপনেয় হলেও, অনপনেয় নয়। আজকের দিনে আফ্রিকাবাসী ছাড়া পৃথিবীর আর কয়জন মানুষই বা স্বগোত্রের খবর জানে? আর কয়জন মানুষই বা স্বদেশের আদি বাসিন্দার বংশধর? যুগে যুগে কত মানুষের ধারা এসে মিশেছে এক এক দেশে। সে-সব মানুষের বংশধরেরা আজ অভিন্ন ধর্মে, ভাষায় ও বর্ণে গড়ে উঠেছে একক জাতিরূপে–হয়েছে অভিন্ন সত্তায় ও আত্মায় বিশ্বাসী। পূর্বপুরুষের মিশ্র ধারার খবরও জানা নেই–অনুভূতি তো দূরের কথা। কাজেই দীর্ঘ সহবাসের ফলে কালে মানুষ একক সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে অভিন্ন সমাজসত্তায় স্বাতন্ত্র্য হারায়। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, যাযাবর জীবনেই ছিল মানুষ অভ্যস্ত। মানুষ স্থিতিকামী হয়েছে খোরপোষের দায়ে ঠেকেই। আজো কী আমাদের অন্তরের গভীরে, সে-যাযাবর তৃষ্ণা জেগে নেই?
আসলে দেশ বলে কোনো মাটির মমতা মানুষের নেই, যা আছে তা পরিচিত মনুষ্য পরিবেশের মোহ। অপরিচয়ের অস্বস্তি, আর পরিচিত পরিবেশের প্রশান্তিই রয়েছে দেশ-বিদেশ চেতনার মূলে। এটাকে ভুল করে আমরা মাটির মমতা বলি। স্বগ্রাম-স্বদেশ আসলে মাটি নয়– মানুষ, যে-মানুষ আজন্ম পরিচিত। এজন্যেই প্রবাসে বন্ধু ও পরিচিতের সংখ্যা বেড়ে গেলে মানুষ সেখানেই স্থায়ীভাব বাস করতে চায়। স্বদেশে শহরে বাসের আগ্রহ ও বিদেশকে ভালবাসার প্রেরণা জাগে প্রীতির প্রসারে ও প্রাবল্যে। অতএব, যে-সব সংস্কার বশে আমরা মানুষের প্রতি বিমুখ ও বিরূপ হয়ে থাকি-তার সব কয়টাই কৃত্রিম। পরিহার করা দুঃসাধ্য নয় মোটেই।
স্বার্থ-বুদ্ধির প্ররোচনাতেই আমরা তিলকে তাল করে তুলি, তুচ্ছকে করি উচ্চ, মোহকে ভাবি মমতা, স্বপ্নকে মানি সত্য বলে।
রাষ্ট্রিক জাতিচেতনা যে নিতান্ত কৃত্রিম, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কেননা রাষ্ট্র ভাঙা-গড়ার সঙ্গে তার জন্ম-মৃত্যু ঘটে। অতএব মানুষে মানুষে মিলনে বাধা কোথায়? আজকের দিনে সরকারি উৎসাহ ও সামাজিক উদারতা থাকলেই দেশে দেশে এ সমস্যার সমাধান কঠিন নয়।
যদি পোশাকে ও নামে দৈশিক ও ধার্মিক ছাপ না থাকে, তাতেও মিলন-ময়দান প্রশস্ত হবে। কুলবাচি পরিহার করলেও অনেকটা ঘুচবে অবাঞ্ছিত ব্যবধান। সবচেয়ে বেশি কার্যকর হবে নির্বিচার বৈবাহিক সম্পর্ক। দেশ-জাত ও বর্ণ-ধর্মের কৃত্রিম বাধা অস্বীকার করে স্ত্রী বা স্বামী গ্রহণের নির্বিঘ্ন রেওয়াজ চালু হলে অখণ্ড পৃথিবীতে একক জাতি ও অভিন্ন সমাজ গড়ে উঠবে। কেননা বিবাহের মাধ্যমেই গড়ে উঠে আত্মীয় সমাজ, আর আত্মীয়তা বোধেই মানুষের কোমলতম ও শ্রেষ্ঠতম বৃদ্ধির বিকাশ সম্ভব হয়। …
যে-সব রাষ্ট্রে গোত্রের, বিভিন্ন ধর্মের, একাধিক ভাষার, নানা বর্ণের ও অনেক সম্প্রদায়ের লোকের বাস; সেখানে একক জাতি গঠনে উক্ত সব নীতি-পদ্ধতি অবশ্যই ফলপ্রসূ হবে। এবং কালে ও ক্রমবিকাশে রাষ্ট্র সীমা অতিক্রম করে এই সমমর্মিতা ও সহযোগিতা বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হবে। এইভাবেই গড়ে উঠবে পুরোনো নামে ও নতুন তাৎপর্যে মনুষ্যজাতি। তখন একক বিশ্বে মনুষ্যজাতির সামগ্রিক সমস্যার সমাধানের জন্যে সমবেত প্রয়াসে উদ্যোগী হবে প্রতিটি মানুষ। তখন বসতি-বহুল অঞ্চল থেকে মানুষ বসতি-বিরল এলাকায় গিয়ে বাস করতে পারবে, জাত-জন্ম ও বর্ণ-ধর্ম বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। কেননা খাদ্য বণ্টনে ও বসতি বিন্যাসে সমতা সাধনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে ভাবী মানুষের সুখ-শান্তি ও আনন্দ-আরাম। মানুষের প্রাণ-ভ্রমরের নিরাপত্তা অর্জন কেবল এ ব্যবস্থাতেই সম্ভব।
রাজনীতি ও গণমানব
০১.
প্রাচীন ও মধ্যযুগে জাতীয়তার স্থান ছিল না, তখন ছিল প্রবল ও পরাক্রান্ত ব্যক্তির রাজ্য ও সাম্রাজ্য। তখন জোর যার, মুলুক ছিল তার। বসুন্ধরা ছিল বীরভোগ্যা। সে-বীরের জাত-জন্ম ও বর্ণ-ধর্ম বিচারের অধিকার ছিল না কারো।
আদিকালের গোত্র-ভিত্তিক সর্দারতন্ত্রই সংস্কৃতি-সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় ক্ষুদ্র ও খণ্ড অঞ্চলভিত্তিক রাজতন্ত্রে এবং আরো পরে সামন্ত সমর্থিত সাম্রাজ্যের বিকাশ লাভ করে। আমাদের পাক-ভারতেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ঐতিহাসিক স্মৃতির যুগে আমরা দক্ষিণ ভারতে যেমন দ্রাবিড় গোষ্ঠীর পল্লব, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের সন্ধান পাই উত্তর ভারতেও তেমনি ইরানী-আর্য ও মধ্য এশিয়ার শক, হুন, কুশান, তুর্কী, মুঘল সাম্রাজ্যের সংস্থিতি লক্ষ্য করি। সবাই বাহুবলেই ভোগ দখল করেছে দেশের ঐশ্বর্য। জনগণের সঙ্গে রাজার সম্পর্ক ছিল শাসকের ও শাসিতের, শোষকের ও শোষিতের। এক্ষেত্রে স্বাজাত্য স্বাধৰ্ম ব স্বাদেশিকতা ছিল অনুপস্থিত।
গোত্ৰ-চেতনা অবশ্যই ছিল, ছিল স্বধর্মী প্রীতিও, আরো ছিল স্ব-ভাষীর প্রতি মমতা। কিন্তু সামাজিক স্তর অতিক্রম করে এসব কখনো রাষ্ট্রিক ঐক্য-বোধের কিংবা আর্থিক স্বার্থবোধের উদ্ভব ঘটায়নি। তাই দত্তশক্তি বিদেশী বিজাতি কিংবা বিধর্মী বলেই তারা কখনো বিক্ষুব্ধ হয়নি। যদিও ধর্মমতের ক্ষেত্রে ও সামাজিক স্তরে বিধর্মী ও বিজাতির প্রতি ছিল অসীম ঘৃণা ও অপরিমেয় বিদ্বেষ। কিন্তু স্বার্থ ও অর্থের ক্ষেত্রে কিংবা শাসন ও শোষণের ব্যপারে তারা দেশ-জাত বা বর্ণ-ধর্ম বিচার করেনি। তাই শক-হূন- কৃশানদেরকে এদেশবাসীরা বিদেশী, বিজাতি কিংবা বিধর্মী বলে প্রতিরোধ করতে এগোয়নি। এমনকি হাজারোর্ধ্ব বছর পরেও তুর্কী, মুঘল বা বৃটিশকেও বিদেশী-বিধর্মী বলে কেউ ঠেকানোর বা তাড়ানোর চেষ্টা করেনি। রাজা বদল ছিল প্রজাদের চোখে অনেকটা এ-যুগের জমিদার বদলের মতোই। কোনো অবস্থাতেই তার অধিক কিছু ছিল না। হাত-বদলের সময়ে খাজনাদির ব্যাপারে জনগণের জীবনে আর্থিক বিপর্যয় ও দুর্ভোগ অবশ্যই ঘটত। কিন্তু তা ছিল সাময়িক। রাজা ছিল শাসক–সেবক নয়। মানুষের উপর তার সর্বাত্মক অধিকার ছিল, তাদের প্রতি দায়িত্ব ছিল না কিছুই। বলতে গেলে একপ্রকারের দায়িত্ব অবশ্যই ছিল, সেটা গৃহস্থের অর্থকর পোষা মেষপাল কিংবা গোধন রক্ষণের ও লালনের দায়িত্বের মতোই। অর্থাৎ রাজস্বের নিশ্চয়তার জন্যে রাজ্যসীমা সুরক্ষিত রাখা ও প্রজাদের শাসনে রাখাই ছিল রাজার দায়িত্ব।
আমাদের এই ধারণার সমর্থনে প্রমাণ অবশ্যই মিলবে। দূর-অতীতের অন্ধকারে না হাতড়িয়ে মধ্যযুগের ভারত থেকেই দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। পর্তুগীজ প্রভৃতি বিদেশী বেনে জাতেরা গোয়া, দামন, দিউ, কারিকল, মাহে দখল করেছিল। এগুলি কোননা-কোনো দেশীয় রাজ্যের এলাকা ছিল। কিন্তু স্বদেশ-চেতনা কিংবা স্বাজাত্য বশে ভারতের কোনো রাজা-বাদশাই তাদের উচ্ছেদ করবার চেষ্টা করেনি। পর্তুগীজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, আর্মেনীয়, ইংরেজ ও ফরাসি বেনেদের সহায়তায় প্রতিবেশীকে জব্দ ও পরাজিত করার চেষ্টা শুরু হয়েছিল ষোলো শতকের গোড়া থেকেই। কারো মনে এ প্রশ্ন কখনো জাগেনি যে তারা নিজেদের কোন্দলে কোনো বিদেশীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে। চোরা কারবারে কিংবা চুরিতে যেমন জাতভেদ নেই, রাজ্য কাড়াকাড়িতেও তেমন জাতধর্মের পার্থক্য চেতনা ছিল না।
কর্ণট দরবারের ঘরোয়া বিবাদে ইংরেজ ফরাসির সাহায্য কামনা; পর্তুগীজ, আর্মেনীয়, ওলন্দাজ ও ফরাসি কর্মচারীর হাতে দেশীয় রাজন্য কর্তৃক রাজ্যরক্ষার ভারার্পণ; টিপু সুলতানকে ইংরেজের বিরুদ্ধে সাহায্যদানে নিযাম-মারাঠার অস্বীকৃতি; পলাশীর যুদ্ধে বিজয়ী ইংরেজকে দিল্লীর সুলতানের দেওয়ানী দান, স্বাধর্মবোধে ভারতের মুসলমান কর্তৃক নাদিরশাহ-আহমদশাহকে মারাঠা দমনার্থে ভারত বিজয়ে প্ররোচনা দান আর নাদিরশাহ-আহমদশাহ কর্তৃক দিল্লী বিজয়, গৃহদ্বারের বিদেশী-বিধর্মী শত্রু ইংরেজকে ছেড়ে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর বালাকোটে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, মীর কাসিম আলির পতনকালে দিল্লীর সম্রাটের ব্রিটিশ পক্ষাবলম্বন, ইংরেজ প্রতিরোধে মারাঠাদের সঙ্শক্তি প্রয়োগে অনীহা, সিপাহীবিপ্লব কালেও দেশী রাজন্যের উচ্ছন্ন-প্রায় ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য প্রভৃতিই সাক্ষ্য দেয় যে রাজা-বাদশাহর দেশ-জাত প্রীতি ছিল না, ছিল কেবল স্বার্থ চেতনা।
তাই সে-যুগের জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে রাজা ও প্রজার সমস্বার্থের কোনো মিলন-ময়দান ছিল না। কাজেই রাজার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের, এবং উত্থান ও পতনের লাভক্ষতি ছিল একান্তই রাজার ও রাজ-পরিজনের ব্যক্তিগত দুর্যোগ-দুর্ভোগের বিষয়। এতে প্রজার কোনো ভূমিকা বা হাত ছিল না। রাজ্য ভাগাভাগির জন্যে দ্বন্দ্ব-মিলনে রাজাদের দেশ-জাত ও বর্ণ-ধর্মের বিচার ছিল না; কেবল সম বা বিষম স্বার্থের গুরুত্ব ছিল। তাই দেশী-বিদেশী বা স্বধর্মী-বিধর্মীর পার্থক্য-চেতনা তাদের চিন্তায় ও কর্মে প্রশ্রয় পায়নি। রাজকীয় ব্যাপারে প্রজাদের অধিকার ছিল না বলেই, এক্ষেত্রে তাদের কোনো দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল না। আর তাই তাদের আনুকূল্য কিংবা প্রতিকূল্যের গুরুত্বও ছিল সামান্য।
পরিণামের পরিপ্রেক্ষিতে পলাশীর যুদ্ধে যে-গুরুত্ব আমরা একালে দিয়েছি, সমকালে এই যুদ্ধের এমনি গুরুত্ব ছিল অভাবিত। ইংরেজ আমলে প্রতীচ্য প্রভাবে লব্ধ জাতীয়তাবাবোধ ও স্বদেশপ্রীতিপ্রসূত এই বোধ আমাদের দেশে অজাতপূর্ব। তাছাড়া স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রে আধুনিক সংজ্ঞানুগত দেশ-জাত চেতনার উদ্ভব ছিল অসম্ভব। এ বোধ জাগে অধিকার ও দায়িত্ব-চেতনা থেকে। রাজকীয় ব্যাপারে প্রজার কোনো অধিকার ছিল না, তাই দেশরক্ষার ও দেশবাসী মানুষের হিতচিন্তার দায়িত্ব ছিল না প্রজার। দায়িত্ব-চেতনাই কৰ্তব বুদ্ধি জাগ্রত করে আর কর্তব্যেবোধই উপায় উদ্ভাবনে প্রবর্তনা দেয়। এতেই ঘটে বোধের বিকাশ, এমনি বিকাশের অন্যতম প্রসূন হচ্ছে স্বাজাত্য ও স্বাদেশিকতা। সেদিনকার রাজন্য ও জনগণের চোখে পলাশীর যুদ্ধ ছিল রাজ্য কাড়াকাড়ির আর দশটা যুদ্ধেরই একটি। তাই ইংরেজের সাফল্যে ভারতীয় রাজন্য- সমাজে কোনো চাঞ্চল্য দেখা যায়নি। দিল্লীর দুর্বল রাজা বরং অর্থলোভে অভিনন্দিত করেছেন ইংরেজদের। শুধু কী তাই! পলাশীর পরেও একশ, বছর সময় পেয়েছিলেন ভারতের রাজারা; কিন্তু ক্রমবধিষ্ণু ইংরেজশক্তিকে ঠেকানোর জন্যে তৈরি হননি কেউ। ভারতের পূর্ব প্রত্যন্ত অঞ্চলের পলাশীর যুদ্ধকে এক বছর পরে ইংরেজ কর্তৃক পশ্চিম প্রান্তের পেশোয়ার বিজয়ের জন্যে দায়ী করা চলে না। এ হচ্ছে ছলনার আশ্রয়ে বিবেককে প্রতারিত করে অক্ষমের আত্মপ্রবোধ লাভের অপচেষ্টা মাত্র।
.
০২.
রাজ্য যে রাজার রাজস্ব উসুলের জমিদারী নয়, জনহিত সাধনের জন্যে সমবায় সংস্থামাত্র–এ সত্যের তত্ত্বগত স্বীকৃতির ভিত্তিতে মধ্যযুগের অবসানে গড়ে উঠেছিল য়ুরোপীয় রাজ্য ও রাষ্ট্রগুলো। এমনি রাষ্ট্রচেতনা সহজে আসেনি। উপলব্ধির এই স্তরে উত্তরণের জন্যে সুদীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম করতে হয়েছে। শোষণ, নির্যাতন ও মৃত্যুর শিকার হয়ে অর্জন করতে হয়েছে এ অধিকার। তাজা প্রাণের, নিউঁকি বুকের পলাশ-লাল রক্তের গঙ্গা বয়ে গেছে য়ুরোপে। এ সাফল্য অর্জন-লক্ষ্যে প্রায় চারশ বছর ধরে ধনে-প্রাণে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে অসংখ্য মানুষকে। মনুষ্য জগতে আধুনিকতা রক্তস্নাত য়ুরোপের দান। চারশ বছরের অনলস অবিরাম সাধনায় লব্ধ এই য়ুরোপীয় জীবন-চেতনা ও জগৎ-ভাবনা তাদের বহির্বিশ্বস্থ উপনিবেশে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে য়ুরোপীয় ভাষার মাধ্যমে।
তেরো শতকের অন্তিমে দান্তের আবির্ভাব থেকেই মধ্যযুগীয় তমসা তরল হতে থাকে। পেত্রার্ক ছিলেন প্রভাতী পূর্বাশা। এমনি করে য়ুরোপ শাস্ত্রের খাঁচা ডিঙিয়ে সাহিত্য-শিল্পের উদার অঙ্গনে মুক্তির স্বাদ গ্রহণ করতে শুরু করে। এভাবে তারা মেরীর চাইতে সত্যকে, যিশুর চাইতে জীবনকে বেশি ভালবাসতে শিখে। এ অঙ্গন যদিও কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না, তবু ইটালীয় শিল্পী-ভাঙ্কর বিজ্ঞানী লিউনার্দো দ্য ভিনসি, রাফেল, মাইকেল এ্যাঞ্জেলো ও টাইটিয়ানের নতুন জীবন ও রূপচেতনা; পনেরো শতকের মাঝামাঝি সময়ে (১৪৫৩ খ্রী.) মুসলিমদের কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের ফলে বাজেন্টাইন গ্রীক বিদ্বানদের য়ুরোপে প্রত্যাবর্তন এবং মুদ্রণযন্ত্রের ব্যবহার এ সাধনাকে অপ্রতিরোধ্য ও বেগবান করে তুলল। তারপর নতুন দেশ আবিষ্কারের প্রভাব প্রসূত reformation ও revolution-এর মাধ্যমে শাস্ত্রীয় Indulgence-এর ফাঁকি ও Inquisition-এর পীড়ন-মুক্ত হয় বহু শতাব্দীব্যাপী নির্যাতিত মানুষ। চারশ বছরব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এই মানববাদ, এই শাস্ত্রদ্রোহিতা, এই সৌন্দর্য-অন্বেষা, এই আত্মবিস্তার, এই বিজ্ঞান বুদ্ধি, এই সম্পদ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় প্রভৃতির সামগ্রিক নাম রেনেসাস। ভাষিক, দৈশিক, রাষ্ট্রিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য-চেতনা তথা জাতীয়তাবোধ এই নবযুগের প্রসূন।
.
০৩.
য়ুরোপীয়দের অন্যান্য উপনিবেশের মতো ব্রিটিশ ভারতেও প্রতীচ্য ভাষা ও বিদ্যার প্রভাবে জাতীয়তাবোধ দানা বাঁধতে থাকে। তবে য়ুরোপে যা ছিল সাধনা ও সংগ্রামলব্ধ, বহির্বিশ্বে তা ছিল অকালে আকস্মিকভাবে অনায়াসপ্রাপ্তি। হঠাৎ করে মধ্যযুগীয় অমানিশা শীত-সকালের কুয়াশার মতো মিলিয়ে গেল। এজন্যে কারো মানসিক, সামাজিক, বৈষয়িক, আর্থিক কিংবা শৈক্ষিক প্রস্তুতি ছিল না। তাই গোড়াতে এই প্রভাব বিচিত্র ও বিকৃত হয়ে দৃশ্যমান হল। পণ্যবিনিময়-ভিত্তিক গ্রামীণ অর্থনীতি আকস্মিকভাবে মৌদ্রিক অর্থনীতির রূপ নিল, প্রতীচ্য বিদ্যায় শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের বিশ্বাস সংস্কারে দেখা দিল দ্বন্দ্ব, শাস্ত্রে ও সাহিত্যে-দর্শনে বিরোধ হল প্রকট, সামন্তবাদ ও পুঁজিবাদের দ্বান্দ্বিক স্থিতি ঘটাল নতুন বিপর্যয়; যন্ত্রচালিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের অভাব, পণ্যের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিদেশী শাসকের শোষণ আনল আয়-ব্যয়ে অসমতা। এক কথায়, মানস কিংবা বৈষয়িক জীবনে কোথাও আর আনুপাতিক ভারসাম্য রক্ষা করা গেল না।
এমনি প্রতিবেশে প্রতীচ্যশিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত মনে জাতীয়তাবোধ এবং তজ্জাত জাতিবৈর অঙ্কুরিত হয়। এ জাতি-চেতনা সুষ্ঠু ছিল না। কখনো ভাষিক, কখনো ধার্মিক, কখনো আঞ্চলিক, কখনো প্রাদেশিক এবং কখনোবা ভারতীয় জাতীয়তারূপে তা আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। এগুলোর মধ্যে স্বধর্ম-ভিত্তিক জাতীয়তাই প্রবল ও প্রকট হয়ে উঠে। রামমোহনে-বিদ্যাসাগরে-বঙ্কিমে এবং হিন্দু-মেলায় এই স্বধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবোধের উন্মেষ যেমন লক্ষণীয়, তেমনি সৈয়দ আহমদ, সৈয়দ আলতাফ হোসেন হালী, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখও ছিলেন মুসলিম জাতীয়তাবাদী।
হিন্দুমনে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করার অবলম্বন হয়েছিল আর্য, রাজপুত ও মারাঠা ঐতিহ্য আর মুসলমানেরা প্রেরণার উৎস করেছিল আরব-ইরানী পুরাণ ও ঐতিহ্যকে। দেশ-কাল-পরিবেশ চেতনা কারো ছিল না। এভাবে তারা কেবল হিন্দু ও নিছক মুসলমান বনেছিল, অর্থাৎ প্যান হিন্দুইজম ও প্যান ইসলামই ছিল তাদের আদর্শিক জাতীয়তার লক্ষ্য। এমনিভাবে দেশকালের প্রয়োজন অস্বীকার করে তারা অতীতে, বিদেশমুখিতায় ও স্বাতন্ত্রে খুঁজেছে স্বস্তি ও শ্রেয়সকে। কল্যাণের পথ তাদের জানা ছিল না, জানতে চায়নি তারা; তাই কল্যাণ আসেনি, সুখ দেয়ওনি, পায়ওনি, কেবল লাভের ও সুখের মরীচিকায় আত্মক্ষয় করেছে।
তারপর এই শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে ব্রিটিশ বিতাড়ন-বাঞ্ছায় কংগ্রেসের ধ্বজা ধরে তারা ময়দানী-মিলনে প্রয়াস পায়। ময়দানী-মিলন বলছি এজন্যে যে তারা আসলে হিন্দু কিংবা মুসলমানই রয়ে গেল, কেবল সমলক্ষ্যে কারখানা শ্রমিকের মতোই সাময়িক স্বার্থে রাজনৈতিক সংগ্রামার্থ মিলন কামনা করেছিল–এ ছিল অনেকটা নীলনদের ধারার মতো। কেননা তারা দেশের সন্তান হিসেবে অভিন্ন সত্তায় ও পরিচয়ে আস্থাবান ছিল না। মুসলিম লীগে ও হিন্দুমহাসভাতেই তাদের চেতনার ও লক্ষ্যের স্বরূপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অতএব, কংগ্রেসী নিবর্ণ জাতীয়তা ছিল অনেকটা ছদ্মরূপ। এবং বিপন্ন খিলাফৎ-প্রীতিই মুসলমানদেরকে কংগ্রেসের সাহায্য প্রত্যাশী করে তোলে। সেই প্রয়োজনের অবসানে: ইংরেজি-শিক্ষিত মুসলমান কংগ্রেস ত্যাগ করে। আর স্বাধীনতাকামী মোল্লা-মৌলভীরা তখনো কংগ্রেসে থেকে যায় হিন্দু প্রীতিবশে নয় অবশ্যই, স্বাধীনতা অর্জনে হিন্দুর শক্তির প্রতি আস্থাবশে। ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমান চাকুরির ক্ষেত্রে ছিল হিন্দুর প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই মুসলিম লীগই ছিল তাদের প্রিয়।
ইংরেজি অজ্ঞ মোল্লা-মৌলভীরা চাকুরির প্রত্যাশী ছিল না, তাই স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দুর সঙ্গে হাত মিলাতে পেরেছিল সহজেই। আবার সেকালের পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা ছিল নগণ্য, তেমনি দাক্ষিণাত্যে ও মধ্য প্রদেশে মুসলমান ছিল বিরল; রাজনীতি ক্ষেত্রে তাই ওদের বিধর্মী-সমস্যা ছিল না, বিধর্মী-বিদ্বেষও ছিল না। শেষাবধি ওসব অঞ্চলে কংগ্রেস প্রভাবও ছিল প্রবল। এদিকে তকালীন যুক্ত প্রদেশে চাকুরি ও জমিদারীর অর্থ-সম্পদের অধিকাংশ ছিল। সংখ্যালঘু মুসলমানদের করতলগত, যেমনটি সংখ্যালঘু হিন্দুর ছিল বাঙলা দেশে।
যুক্ত প্রদেশের মুসলমান এই স্বার্থ ও সুবিধা দীর্ঘস্থায়ী করবার জন্যে সচেষ্ট ছিল। তাদের নেতৃত্বে ও বাঙালির সংগ্রামে পাকিস্তান অর্জিত হয়েছিল। মোটামুটিভাবে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ওহাবী সংগ্রামের অবাসনে স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে উত্তর-পূর্ব ভারতে ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু-দ্বেষণা ও ব্রিটিশ-প্রীতি প্রবল হতে থাকে। হিন্দু-বিদ্বেষের মূল ছিল সরকারি অনুগ্রহের প্রত্যাশা। অতএব, ১৮৬০ সন থেকে ১৯৪৭ সন অবধি ইংরেজি শিক্ষিত মুসলমানেরা স্বাধীনতা-সংগ্রামী ছিল না, সরকারি সহযোগিতায় হিন্দুর কবল থেকে নিজেদের প্রাপ্য ধন-সম্পদ উদ্ধারেই ছিল ব্রতী। সে ধন-সম্পদ অবশেষে পাকিস্তান রাষ্ট্ররূপে আয়ত্তে এল।
যে ভাগ-বাটোয়ারার দাবী উনিশ শতকের শেষ পাদ থেকে উত্তর-পূর্ব ভারতের মুসলিম-মনে গুঞ্জরিত হচ্ছিল, তা-ই মুসলিম লীগের মাধ্যমে প্রবল ও ফলপ্রসূ হল। মূলত হিন্দুর জন্যে হলেও কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা চেয়েছিল। ব্রিটিশ বিতাড়নে সাফল্য আসে কংগ্রেসের মাধ্যমেই। তার আনুষঙ্গিক ফল পাকিস্তান।
.
০৪.
ব্রিটিশ যুগে কিছুসংখ্যক বর্ণহিন্দু চাকুরে-মহাজন-জমিদার বাঙলার অর্থ-সম্পদ করায়ত্ত করে। বর্ণ ধর্ম অবিশেষে আর সব বাঙালিই ছিল নির্জিত, শোষিত ও নির্যাতিত। ইংরেজি শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত বর্ধিষ্ণু মুসলিম সমাজ দেশের ধন-সম্পদে, বাণিজ্যে ও চাকুরিতে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়ে ওদের প্রতিপক্ষতা শুরু করে। এ ছিল স্বস্বার্থে সমশ্রেণীর প্রবল শোষকের বিরুদ্ধে দুর্বল বঞ্চিত শোষকের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এর মধ্যে গণ-কল্যাণের কোনো অভিপ্রায় ছিল না। চাকুরি-সদাগরী জমিদারীতে শিক্ষিত মুসলমানের আনুপাতিক হার প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলিম জনগোষ্ঠী শোষণ ও দারিদ্র্যমুক্ত হত না। যেহেতু চাকুরে-মহাজন-জমিদার ছিল হিন্দু, সেহেতু এইসব উচ্চাভিলাষী মুসলমান স্বধর্মীর অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের সুযোগে স্বস্বার্থে মুসলিম মনে জাতিবৈর জাগাতে সমর্থ হল সহজেই। ফলে শোষক-শোষিত নির্বিশেষ হিন্দুর প্রতি মুসলিম-মনে জাগল ক্ষোভ ও বিদ্বেষ। গণ কল্যাণে যে-সংগ্রাম শুরু হওয়া উচিত ছিল ব্রিটিশ শাসক ও দেশী শোষকের বিরুদ্ধে, তা এভাবে বিধর্মী-বিদ্বেষের রূপ নিল। গণমানবের অজ্ঞতা ও সরলতার সুযোগে মুসলিম লীগ গণ-সমর্থনে অর্জন করল পাকিস্তান। যারা পূর্বে ধন-সম্পদ দখলে ছিল হিন্দুর পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বী, পাকিস্তানে তারাই হল পরিত্যক্ত ধন-সম্পদ চাকুরির নির্ঘ ও নির্বিঘ্ন মালিক। জনগণের দুর্ভাগ্য-দুর্ভোগ রইল পূর্ববৎ।
.
০৫.
এদিকে কালক্রমে পাকিস্তান প্রাপ্তির প্রাথমিক উচ্ছ্বাসে ও উল্লাসে যখন ভাটা পড়েছে, তখন ক্রমবর্ধিষ্ণু শিক্ষিত বাঙালিরা দেখছে তারা অর্থ-সম্পদের সর্বক্ষেত্রে ঠকছে। তাদেরই স্বস্বার্থে তারা আবার পূর্বতন নীতিরই অনুবর্তন কামনা করছে রাজনীতিক্ষেত্রে। তারা দেখছে চাকুরি ও ব্যবসা ধনাগম, ও মর্যাদার এই দু-ক্ষেত্র তাদের হাতছাড়া, সেখানে প্রবেশাধিকার বর্তমান অবস্থায় একরকম অসম্ভব। পাকিস্তান যখন হল তখন সামরিক বিভাগে বাঙালি ছিলই না, প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও পদস্থ বাঙালি মুসলিমান ছিল নেহাত নগণ্য। আর ব্যবসা-বাণিজ্যে তাদের ছিল অনীহা ও আর্থিক অসামর্থ্য। বিশেষ করে হিন্দু-বিদ্বেষজাত বেরাদরী উদারতা বশে তখন বাঙালিরা ন্যায্য প্রাপ্য দাবি করেনি। না-পেয়েও তারা পাওয়ার আনন্দে ছিল অভিভূত। আগে জাতি- দ্বেষণাবশে তারা ছিল বেরাদরী-ভাবে বিভোর। ইদানীং দারিদ্র্য, শোষণ ও হতবাঞ্ছার আঘাতে শিক্ষিত বাঙালি আবার স্বাধিকার সংগ্রামে অবতীর্ণ। আগে গণসমর্থন লাভের জন্যে তাদের অবলম্বন হয়েছিল হিন্দু দ্বেষণা, এখন তারা উত্তেজনা দানের ইন্ধন করছে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও.ভাষিক স্বাতন্ত্র্যকে। পূর্বে মুসলিম মনে হিন্দু-বিদ্বেষ যেমন করে প্রবল হয়েছিল, অবিকল তেমনি ধারায় ও তেমনি যুক্তিতে দানা বাঁধছে উর্দুভাষী-বিদ্বেষ। কেবল প্রতিপক্ষ বদল হয়েছে, উপায় ও উদ্দেশ্য রয়েছে অবিচল। এর মধ্যেও পূর্বেকার ফাঁক ও ফাঁকি উভয়েই বর্তমান।
পাকিস্তানের শিল্প-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করে বোম্বাই থেকে আগত মেমন ও ইসমাইলী সম্প্রদায়, সামরিক ও বেসামরিক বড় চাকুরিগুলো রয়েছে পাঞ্জাবী ও উত্তর ভারত থেকে আগত মোহাজেরদের হাতে। মেমন ও ইসমাইলী ধনপতি-পুঁজিপতিদের পরিচয়ও জানে না বাঙালিরা, তারা চোখের সামনে দেখে পাঞ্জাবী বড় সাহেবদের। পশ্চিম পাকিস্তানী বলতে এরা সিন্ধি, বেলুচ, পাঠান, মোহাজের-ভেদ মানে না, তাদের চোখে সবাই উর্দুওয়ালা ও পাঞ্জাবী। এমনকি বাঙলার বিহারী মোহাজেরেরাও উর্দুওয়ালা বলে বিহারী-পাঞ্জাবী তাদের কাছে সমার্থক।
এখানকার বিহারীদেরও দোষ আছে। ভাষিক ঐক্যের দরুন তারা পাঞ্জাবীদের মনে করে জ্ঞাতি এবং পাঞ্জাবী শাসনকে তারা ভাবে নিজেদেরই শাসন, ফলে ইংরেজ আমলের দেশী খ্রীস্টান। ও এ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের মতো তারাও নিজেদের মনে করে শাসকজাত। আর পশ্চিম পাকিস্তানীর স্বার্থ, লাভ ও গৌরবের তারাও যেন অংশীদার। সেজন্যে বাঙলার বিহারী মোহাজেরেরা। রাজনীতিক্ষেত্রে এ অংশের স্বার্থে কিছু তো করেই না, বরং তাদের আনুগত্য থাকে করাচি-লাহোর রাওয়ালপিণ্ডির প্রতি। এভাবে তারা নিজেদেরকে নিজেরাই বিপন্ন করছে। আর মধ্যবিত্ত নামে পরিচিত উঠতি বাঙালি বুর্জোয়া এবং চাকুরেরাও তাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা মানসে পূর্বের মতো এ. সুযোগ গ্রহণ করে উর্দুওয়ালা নামে অভিহিত অবাঙালি মাত্রেরই বিরুদ্ধে অজ্ঞ-দরিদ্র জনগণকে লেলিয়ে দিতে উৎসুক। স্ব-স্বার্থেই এই বিকাশমান বাঙালি সমাজ প্রতিদ্বন্দ্বী অবাঙালি পুঁজিপতি ও চাকুরেদের সম্পদে ও সম্মানে ভাগ বসাতে চাচ্ছে–বাঙালি জনগণের স্বার্থে নয়।
আযাদী-উত্তর যুগে হিন্দু চাকুরে-মহাজন-জমিদার ও ব্যবসায়ীর স্থলে শিক্ষিত মুসলমান শ্রেণী বসে মজা লুটছে, জনগণের তকদির রয়েছে অপরিবর্তিত। এও তেমনি এক চাল, এখন যেমন বিশ-বাইশটি অবাঙালি পরিবার পাকিস্তানের ধন-সম্পদের মালিক, তখন ছিল তেমনি কয়েকজন হিন্দু-জৈন আগরওয়ালারা। আগে যেমন হিন্দু শোষক শ্রেণীর সঙ্গে লড়তে গিয়ে আপামর হিন্দুর। বিরুদ্ধে বিদ্বেষ-বিষ ছড়িয়েছে তারা, এখন আবার তেমনি পুঁজিপতি ও চাকুরে পশ্চিমাদের থেকে সম্পদ-সম্মানের ভাগ আদায় করবার জন্যে আপামর অবাঙালি-দ্বেষণা জাগানোর চেষ্টা চলছে। এর নাম বাঙালির স্বাতন্ত্র্য-চেতনা, নামান্তরে বাঙালির জাগরণ। উঠতি মধ্যবিত্তের স্বার্থে এ আন্দোলন গড়ে উঠছে বলেই এতে আমাদের আপত্তি।
.
০৬.
নইলে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তা ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা অনেকেরই মনঃপূত নয়। সমস্বার্থে মিলন অসম্ভব নয়। বটে, তবে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা যে আর্থিক, ভাষিক, সাংস্কৃতিক ও জীবনধারণ পদ্ধতির পার্থক্য ঘটায়, তাতে আধুনিক রাষ্ট্রভিত্তিক জাতীয়তাও নিতান্ত কৃত্রিম ও অকেজো হয়ে পড়ে। এ কারণে, একক রাষ্ট্র-গঠনে কিছুসংখ্যক লোকের আপত্তি গোড়াতেই শোনা গিয়েছিল। কিন্তু তখন সাফল্য ও প্রাপ্তির উল্লাস বশে কেউ স্বস্থ ছিল না, তাই এ সদ্বুদ্ধি তখন পাত্তা পায়নি।
বাঙালির সর্বাত্মক স্বাতন্ত্র্য ও স্বার্থ রক্ষিত হোক, তা আমাদেরও কাম্য। কিন্তু তা জনস্বার্থে ও জনকল্যাণের জন্যেই হওয়া চাই,অবাঙালি বুর্জোয়াকে তাড়িয়ে বাঙালি বুর্জোয়ার সুবিধে করে দেবার জন্যে নয়। আগে একবার বেরাদরানে ইসলাম-এর মোহে পড়ে ঠকেছি, আবার বাঙালি ভাইয়ের মমতায় পড়ে প্রতারিত হতে চাইনে। স্বার্থের জন্যে আমরা বাপ-ভাইয়ের সঙ্গে দ্বন্দ্ব করতে দ্বিধা করিনে। বাঙালি ভাইকে পুঁজিপতি ও ধনপতি করবার জন্যে নিজের প্রাণ দেবার মতো নির্বোধ থাকা এ-যুগে নৈতিক অপরাধ ও শোচনীয়রূপে বেদনাকর। জনগণের এমনি অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্যের সুযোগে চিয়াঙকাইশেকরা চীনে রাজত্ব করেছিল; স্বদেশী স্বজাতি বেরাদরের শোষণ থেকে গণমানব মুক্তি খুঁজেছিল অন্য পন্থায়। চিয়াঙকাইশেকরাও সেদিন গণস্বার্থ রক্ষার ভাওতা দিয়ে বিদেশী বিতাড়নে জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনে হয়েছিল গণনেতা। তারপর ক্ষমতা হাতে পেয়ে তারা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে।
আর গণমানবেরা দেখল তারা প্রতারিত, শোষিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত এবং স্বদেশী ও বিদেশী শাসনে পার্থক্য নগণ্য। স্বদেশী বা বিদেশী শাসন এ-যুগে বড় সম্পদ বা সমস্যা নয়, এ-যুগে বঞ্চক বঞ্চিত সম্পর্ক সব সমস্যার মূলে। বঞ্চিত জনের কল্যাণ চিন্তাই, তার শোষণ ও দারিদ্র মুক্তিই এ যুগের রাষ্ট্র-ভাবনার একমাত্র বিষয়। বুর্যোয় স্বার্থের সংগ্রামকে গণ-সংগ্রাম বলে চালিয়ে দেয়ার দিন অপগত-প্রায়–এই প্রত্যয় নিয়ে মানুষের রাষ্ট্র-সাধনা ও রাজনৈতিক সংগ্রাম গণ-মুক্তি ও গণ কল্যাণে নিয়োজিত হবে–এই আশ্বাসে ও অঙ্গীকারে আমরা সুদিনের প্রতীক্ষারত।
শিল্প-সাহিত্যে গণরূপ
জীবন আছে অথচ প্রয়োজন নেই, এমন হতেই পারে না। আমি আছি বলেই আমার ভুবন আছে। আমার জীবন সেই ভুবনের সঙ্গে একই নাড়িতে যুক্ত, একই সূত্রে গাঁথা। আমার জীবনের তুচ্ছ উচ্চ সর্বপ্রকার প্রাত্যহিক কিংবা মৌর্তিক প্রয়োজন আমার ভুবনই মিটায়। আমি আছি তাই আমার পেটের ভাত, পরনের কাপড়, রোগের প্রতিষেধক, শোকের প্রবোধ, দেহের পুষ্টি ও মনের তুষ্টির দরকার। রুচি বদলের জন্যে আমি বন্ধনে মুক্তি, যন্ত্রণায় আনন্দ, সমস্যায় সমাধান যেমন সন্ধান করি; তেমনি কখনো কখনো মুক্তি এড়িয়ে বন্ধনকে, আনন্দকে হেলা করে যন্ত্রণাকে, সম্পদ ছেড়ে সংকটকে বরণ করে জীবনের অন্য স্বাদ খুঁজি।
জীবন আমার কাছে কখনো দায়িত্ব, আর কখনো বিলাস, কখনো দায়, কখনো সম্পদ, সকালে আনন্দ আবার সন্ধ্যায় যন্ত্রণা, কখনো খেলনা কখনো ঐশ্বর্য, কখনো বোঝা, কখনো পাথেয়, কখনো বেদনা, কখনো বা আকুতি, কখনো প্রাণময়, কখনো মনোময়, কখনো রূঢ়িক, কখনো সামাজিক, কখনো বৈষয়িক, আবার কখনো বা দার্শনিক। সবটা মিলে জীবন এক অনন্য অনুপম দুর্লভ ঐশ্বর্য। এই জীবনের স্বাদ যে একবার সচেতনভাবে পায়, সে আনন্দলোকেরই সন্ধান পায়। জীবন-ধনে যে ধনী, তার কাছে নিখিল জগৎ রূপবান হয়ে অপরূপ হয়ে আবির্ভূত হয়। সেই রূপসী ধরণীর অনুরাগে তার স্বভাবে আসে কমনীয়তা, তার হৃদয়ে জাগে ঔদার্য, প্রীতির সঞ্চয়ে ভরে উঠে তার বুক। চিত্তলোকে তার গড়ে উঠে মাধুর্যের মৌচাক। তখন সে প্রীতি ও শুভেচ্ছার পুঁজি নিয়োগ করে। তার ভুবনে। বিনিময়ে পায় মানুষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা। জীবনে এর চেয়ে বড় সম্পদ, এর চেয়ে কেজো পাথেয় আর নেই। মানব জমিন আবাদ করলে যে ফসল মেলে, তা কখনো নিঃশেষ হয় না–বন্ধ্যা হয় না।
মন-প্রাণের এমনিধারা অনুশীলনের নামই সংস্কৃতিচর্যা, আর এ স্তরে উত্তরণই সংস্কৃতি। এমনি করে সংস্কৃতিবান হলেই মানুষ হয় প্রীতিপরায়ণ, সংবেদনশীল, পরিণামদর্শী ও কল্যাণপ্রবণ। কেননা, সে বোঝে–নগর পুড়লে দেবালয় এড়ায় না, একে নষ্ট করলে সবাই দুঃখ পায়। এমন মানুষ অনুকম্পা বশে উদার হয় না, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধে মহৎ হয়। তেমন মানুষ বাদশা কিংবা ফকির হতে পারে, চালু অর্থে মূর্খ কিংবা জ্ঞানী হতে পারে, নিরক্ষর কিংবা বিদ্বান হতে পারে। কিন্তু তাতে তার মানবিক চেতনায়, তার প্রীতিশীলতায়, তার হিতবুদ্ধিতে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। অবশ্য তা ব্যক্ত হওয়া কিংবা অব্যক্ত থাকা, তার সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা নির্ভর করে তার সামাজিক, শৈক্ষিক, আর্থিক ও ধার্মিক প্রতিবেশের উপর। কিন্তু তাতে তার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের ঔজ্জল্য কমে না, বরং অবরুদ্ধ আবেগের বেদনায় তপ্ত কাঞ্চনের মতো–কষিত সুবর্ণের মতো তার রূপ, তার লাবণ্য বাড়ে।
এমন মানুষ যখন লোকসেবায় নামে তখন সে বুদ্ধ-যীশু-কবীর-নানক-চৈতন্য-বায়যিদ হয়, যখন নৃপ হয় তখন ইউসুফ-রাম-নওশেরোয়া হয়। যখন লিখিয়ে হয় তখন শেপীয়র ভল্টসয়ার গ্যটে-টলস্টয়-লা-রবীন্দ্রনাথ হয়। যখন গাইয়ে-বাজিয়ে হয় তখন তানসেন-হরি বৈজু-বিটোফন হয়। যখন আঁকিয়ে-বানিয়ে হয় তখন ভিঞ্চি-এ্যাঞ্জেলো-পিকাসো হয়– তখন আমরা পাই অজন্তা ইলোরা-এথেন্স-আগ্রার ভাস্কর্য, স্থাপত্য ও আলেখ্য। যখন দার্শনিক হয় তখন তার মধ্যে প্ল্যাটো এ্যারিস্টোটল-রুশদ-হেগেল-নীৎসে-সার্জেকে পাই। যখন সমাজতাত্ত্বিক হয় তখন সেন্ট অগাস্টাইন খলদুন-মার্কসকে পাই। যখন বিজ্ঞানী হয় তখন ডারউইন-ফ্রয়েডকে পাই। যখন বিপ্লবী হয় তখন লেনিন-মাও-গুয়েভারাকে দেখি। এ যুগে যন্ত্র-প্রভাবে মানুষের জীবিকা ও জীবন-পদ্ধতি পালটে গেছে। তাই যুগ-প্রয়োজনে গণচেতনা, গণসাহিত্য ও গণতন্ত্রের কথাই প্রাত্যহিক জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে প্রায় সর্বক্ষণ শুনতে হয় আমাদের।
যন্ত্রায়ত জীবিকার ফলে উদ্ভূত জীবন-প্রতিবেশে আত্মপ্রত্যয়ী মানুষ আজ আর আগের মতো আসমানের দিকে তাকিয়ে থাকে না। সে এখন দৈব-নির্ভর নয়, রোদ-বৃষ্টি-রোগ-অন্নের জন্যে ভাগ্যের উপর ভরসা রাখে না। সে বুঝেছে এতে প্রকৃতির প্রভাব যতটুকু, তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি রয়েছে মানুষের হাত। মানুষের লোভ, স্বার্থপরতা ও অপ্রেম-অবিবেচনাই মানুষের দুর্ভোগ ও মৃত্যুর কারণ। কাজেই স্বায়ত্ত জীবন ও জীবিকার নিরাপত্তা, সুষ্ঠু বিন্যাস ও সুনিয়ন্ত্রণের কথাই সে সর্বক্ষণ ভাবছে, না-ভেবে পারছে না। তার অন্ন চাই, আনন্দ চাই, ওষুধ চাই, প্রবোধ চাই। প্রাচুর্যহীন কাড়াকাড়ির যুগে তাই মানুষকে শোষণ, পীড়ন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। তারা অক্ষম বলেই তাদের সৈনাপত্য নিয়েছে সংবেদনশীল মানববাদী লোকসেবক, লেখক, গায়ক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি সবাই। এই লড়িয়ে লোকগুলোই স্ব স্ব ক্ষেত্রে লড়াই করে যাচ্ছে মানুষের মুক্তির জন্যে। তারা মুক্তি কামনা করে শোষণ থেকে, অশিক্ষা থেকে, দৈন্য থেকে, বিশ্বাস থেকে, সংস্কার থেকে, পীড়ন থেকে, অন্ধকার থেকে, অজ্ঞতা থেকে, অমঙ্গল থেকে, হীনমন্যতা থেকে।
এদের মধ্যে যারা লিখিয়ে তারা গণসাহিত্যিক, যারা নেতৃত্ব দেয় তারা গণনেতা, যারা আঁকে তারা গণশিল্পী, যারা চিন্তাবিদ তারা মানববাদী, যারা ঐতিহাসিক তারা সমাজতাত্ত্বিক। এ সংগ্রাম চলছে লেখা ও রেখার, কথা ও সুরের মাধ্যমে। তারা লিন্দু শোষক ও পীড়কদের মনের কাছে, মস্তিস্কের কাছে, বিবেকের কাছে এ আবেদনই জানাতে চাচ্ছে যে–পরিণামদর্শী হও, বিবেকবান হও এবং সংবেদনশীল হও, আর আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই যৌথ জীবনের সুখ-দুঃখ, লাভ-ক্ষতি সমভাবে ভাগ করে নিতে এগিয়ে এসে, নইলে নিষ্কৃতি নেই তোমার–যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে টানিছে যে নীচে। সমস্বার্থের ভিত্তিতে সহযোগিতা ও সহঅবস্থানে রাজি হতেই হবে। এরই নাম গণসাহিত্য, গণসংগীত ও গণশিল্প। কাজেই গণশিল্প-সাহিত্য, শোষিত-পীড়িত অন্ধ-অশিক্ষিত চাষী-মজুরের জন্যে নয়, পীড়ক-শোষক লিন্দু বেনে বড় লোকের উদ্দেশ্যেই রচিত।
আমার লেখায় ও রেখায়, আমার কথায় ও সুরে আমার জীবনের চাহিদার দাবি; আমার ভাত-কাপড়ের, আমার তেল-নুন-লাকড়ির, আমার ওষুধ-পথ্যের অভাবের কথাই অভিব্যিক্ত পাবে। কেননা এ অভাব আমাকে সর্বক্ষণ ঘিরে রয়েছে, আমার জাগ্রত মুহূর্তগুলো বিষিয়ে তুলেছে; আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। যন্ত্রণার প্রকাশপথ রুদ্ধ করা সহজও নয়, স্বাভাবিকও নয়। এই যন্ত্রণার অভিব্যক্তি ও তার নিরসনের আবেদন ও আকুতিই গণশিল্প-সাহিত্য বা সঙ্গীত। অভাবজীর্ণ পাঁজর থেকে এ ছাড়া আর কী আশা করা যায়! আজো তকদির-বাদী ও নিয়ন্ত্রিত জীবনে যারা আস্থা রাখে আর যারা অন্যের শোণিত পানে পুষ্ট, অথচ যাদের সংবেদনশীলতা কিংবা পরিণামদর্শিতা নেই, কেবল তাদের মুখেই আমরা শুনতে পাই আদ্যিকালের ফুল-পাখি ও প্রেম-প্রকৃতির মহিমা কীর্তন।
এ শতক মানুষের মুক্তির বাণী বয়ে নিয়ে এসেছে। অজ্ঞতা থেকে, দাসত্ব থেকে, পরাধীনতা থেকে, দারিদ্র্য থেকে, লিপ্সা থেকে, অমানুষিকতা থেকে প্রত্যহ মুক্তি আসছে কারো-না-কারো, কোথাও-না-কোথাও। অতএব শতাব্দীর আহ্বান ব্যর্থ যাবে না। আলো ঝলমল আনন্দঘন সুপ্রভাত আসন্ন। সামনে নতুন দিন।
সংস্কার-সততা-সাহিত্য-প্রজ্ঞা-শিক্ষা
ধর্ম বলতে সাধারণে যা বোঝে তা এমন একটি সংবিধান, বুদ্ধিমানের দ্বারা প্রবর্তিত আর নির্বোধ দ্বারা অনুসৃত। এ এমন একটা idea দেয়, এমন একটা চেতনা দান করে যা শৈশবে, বাল্যে ও কৈশোরে–প্রত্যয়ের ও প্রথার, বিশ্বাসের ও ভরসার, স্বস্তির ও সংস্কারের এক অক্ষয় পাথুরে কেল্লা নির্মাণ করে। সামুক-কুর্মের দেহাধারের মতোই এটি মানুষের সংস্কারার্জিত চেতনাকে সারাজীবন সযত্নে রক্ষা ও নিয়ন্ত্রণ করে।
ফলে অতিক্রান্ত কৈশোরে মানুষ যা-কিছু দেখে বা শুনে, তা ঐ কেল্লার বাইরে মরিচার মতো, ধূলিস্তরের মতো কিংবা আবরণ-আভরণের মতোই সংলগ্ন থাকে মাত্র, চেতনায় সমন্বিত হয় না। এজন্যেই অর্জিত বিদ্যা, লব্ধ জ্ঞান, উদ্ভূত প্রজ্ঞা মানুষের বৈষয়িক জীবনে কেজো বটে, কিন্তু অন্তৰ্জীবনে ব্যর্থ।
ব্যবহারিক জীবনে বিদ্যা-জ্ঞান-প্রজ্ঞার উপযোগ ও প্রয়োগসাফল্য প্রত্যক্ষ। তাই এগুলো সর্বথা ও সর্বদা বহুল প্রযুক্ত। কিন্তু অন্তৰ্জীবনে–ভাবলোকে এগুলো প্রবেশপথ পায় না। তাই মানুষের এতকালের জ্ঞান-গবেষণা, বিদ্যাবত্তা ও প্রজ্ঞা-প্রদীপ মানুষের বৈষয়িক জীবনে যতটা স্বাচ্ছন্দ্য ও সাফল্য দিয়েছে, তার সিকি পরিমাণও বিস্তৃত কিংবা ভাস্কর করেনি অন্তর্জগৎ। সেজন্যে আজো মানুষ প্রাণের পরিচর্যাই কেবল করে, বিবেকের অনুশীলনে উদ্যোগী হয় না। ফলে মন-রথীর বিবেক-সারথি ছিন্ন-বল্প অশ্বের প্রতীয়মান নিয়ন্তামাত্র। তাই জগৎ-সংসার এক বিরাট বিচিত্র খেদার রূপ নিয়েছে। বাহ্যত সব বাঁধনই যেন ফসূকে গেরো, কিন্তু তবু মুক্তি অসম্ভব। খেদায় হাতীর বল-বীর্য-বুদ্ধি কোনটাই কাজে লাগে না। প্রথম জীবনে ঘরোয়া পরিবেশে নির্মিত প্রত্যয়ের এবং প্রথার খেদায়ও মানুষের অর্জিত বিদ্যা-বুদ্ধি ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা মানুষের মুক্তির সহায় হয় না। অনুগত হাতীর পীড়নে বুনো হাতীর জীবন যেমন পারবশ্যতায় অপচিত, তেমনি পুরোনো সমাজ সংস্কারের আনুগত্যে ভূমিষ্ঠ মানুষ পোষাপ্রাণীর যান্ত্রিক জীবন-ভাবনায় বিড়ম্বিত।
মুক্তির উপায়-লব্ধ-প্রত্যয় ও প্রথা পরিহারের অঙ্গীকারে অর্জিত জ্ঞান, উদ্ভূত প্রজ্ঞা ও অনুশীলিত বিবেকের প্রাধান্য দান। তাহলেই কেবল আত্মায় ও আত্মীয়ে, স্বভাবে ও সংসারে, প্রজ্ঞায় ও প্রত্যয়ে, জীবনে ও জগতে, বিদ্যায় ও বিশ্বাসে, বিবেকে ও বিষয়ে দ্বন্দ্ব ঘুচবে। নৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক কিংবা বৈষয়িক জীবনে বিরোধ ও বিবাদ কমবে–অন্তত তা তার জীবন-বিনাশী প্রাবল্য হারাবে।
সততা
সততা তিন প্রকার: পাপভীরুতা জাত, পার্থিব শাস্তিভীরুতা জাত এবং আত্মসম্মান ও আদর্শ প্রসূত। প্রথম দুটো সাহসের অভাবজনিত। আর তৃতীয়টি যথার্থ চরিত্রবলের অবদান। প্রথম দুটোর সামাজিক প্রভাব সামান্য, কেননা ঐরূপ সততা ব্যক্তিত্ব দান করে না। শেষোক্তটির প্রভাব সামাজিক মানুষের নৈতিকচরিত্র উন্নয়নের সহায়ক। কেননা, আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন তেমন মানুষের ব্যক্তিত্ব তার চারদিককার মানুষকে প্রভাবিত করে এবং তাকে অনুসরণের প্রেরণা দেয়। এমন মানুষের সততা নির্ভীকতাপ্রসূত এবং তা ক্ষতি স্বীকারের ও যন্ত্রণা সহ্য করবার শক্তিদান করে। এমন সতোর ভিত্তি নির্লোভ, আদর্শচারিতা ও মর্যাদা-চেতনা। পাপ ও কলঙ্কভীরুতা একপ্রকার Negative ব্যক্তিত্ব, পক্ষান্তরে নিজের মর্যাদা-চেতনা একটি Positive গুণ।
পাপ-ভয় কিংবা নিন্দা-কলঙ্ক-শাস্তি ভয় জাগিয়ে মানুষকে সৎ রাখা সহজ নয়। বিশেষ বয়সে প্রবল প্রলোভনের তোড়ে পাপ-ভয়জনিত সততা স্রোতের মুখে কুটোর মতোই ভেসে যায়। আর গোপনে অপকর্ম করে সহজেই নিন্দা-কলঙ্ক-শাস্তি থেকে নিষ্কৃতি মেলে। যখনই সুযোগ মিলবে, সতোর মুখোশ পরিহার করতে মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হবে না। সামাজিক জীবনে সততা স্থায়ী করতে হলে পাপ ও নিন্দা-ভীরুতার ভঙ্গুর বাঁধনে আস্থা রাখা চলবে না। মানুষের অতীত ইতিহাসই তার সাক্ষ্য। কেবল মর্যাদাবোধের দৃঢ় ও ধ্রুব ভিত্তিতেই সতোর অনুশীলন ও প্রতিষ্ঠা সম্ভব। আর আইন ও শাসনের কঠোরতায় কোনো স্থায়ী ফল মেলে না। ওটি আপাত উপশমের উপায়মাত্র। . আসলে সমাজে প্রতিষ্ঠাকামী না হলে মানুষের মনে সততা-প্রীতি স্থায়ী হয় না। এজন্যে কিছু শিক্ষা, কিছু আর্থিক স্বাচ্ছল্য এবং সমাজে গণ-জীবন উন্নয়নের ও বিকাশের কিছু সুযোগ থাকা প্রয়োজন। সামন্ত-প্রধান সমাজে তা ছিল প্রায় অনুপস্থিত। বুর্জোয়া সমাজে ধনের ও পদের মর্যাদা আর সর্বপ্রকার মূল্যবোধকে ছাপিয়ে উঠে বলে সেখানেও সতোর সুপ্রসার সম্ভব নয়। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থাতেই মানুষের সততা ও আদর্শ-চেতনা প্রবল ও প্রকট হয়ে উঠতে পারে। কাজেই নৈতিক জীবনের মানোন্নয়নকামীরা অন্য উপায়ে অভীষ্ট ফল পাবেন না। কেবল সাফল্য মরীচিকায় আশ্বস্ত থাকবেন মাত্র।
নিঃস্ব লোকের আকাক্ষা প্রয়াস-প্রেরণা যোগায় না–তা বন্ধ্যা। তেমন লোক প্রাণে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টায় থাকে, পাপ-পুণ্য কিংবা নিন্দা-লজ্জামানের কথা ভাবে না। তা তার পক্ষে অসম্ভব ও অনর্থক জেনেই সে উদাসীন কিংবা বেপরওয়া। সমাজে প্রতিষ্ঠা যে পাবেই না, সে কেন নিন্দা লজ্জার ভয় করবে? সৎপথে যার জীবিকা অর্জন সম্ভবই নয়, পুণ্যের প্রত্যাশা তার ত্যাগ করতেই হবে। অতএব ধর্ম বল, নীতিবোধ বল, পুণ্য বল আর মান বল, সবই আর্থিক স্বাচ্ছল্য ও সামাজিক, প্রতিষ্ঠা-বাঞ্ছা থেকেই উৎসারিত।
সাহিত্য
মানুষের জীবন-চেতনার ও জীবন-চর্যার পরিচয় তার আচরণে, সাহিত্যে, শিল্পে, সঙ্গীতে, ভাস্কর্যে ও স্থাপত্যে অভিব্যক্তি পায়। সে-প্রকাশ কখনো অকৃত্রিম হয় না। কেননা সমাজবদ্ধ প্রতিটি মানুষই নানা অদৃশ্য বন্ধনের বান্দা। তার জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় দেশ, কাল, ধর্ম, আচার, বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতির প্রভাবে। তাই মানুষের মন ও মেজাজ, লোভ ও ক্ষোভ, ন্যায় ও অন্যায়বোধ, রুচি ও শ্রেয়োচেতনা স্থান-কাল-পাত্র সংপৃক্ত ও আপেক্ষিক। কখনো স্বার্থচেতনা, কখনো হিতবোধ, কখনো গৌত্রিক স্বার্থ, কখনো জাতিক আদর্শ, কখনোবা মানবিক-চেতনা প্রবল হয়ে মানুষের চিন্তা ও কর্ম নিয়ন্ত্রণ করে।
ষড়রিপুর প্রেরণায় যেমন সে পরিচালিত, তেমনি কোনো আদর্শ এবং নৈতিক দায়িত্ব আর কর্তব্যবোধও তাকে চিন্তায় ও কর্মে প্রবর্তনা দেয়। ইন্দ্রিয় ও অতীন্দ্রিয়ের বিপরীতমুখী আকর্ষণেও মানুষের ভাব-চিন্তা-আচরণে দ্বান্দ্বিক অসঙ্গতি প্রমূর্ত হয়ে উঠে। এজন্যে সামাজিক মানুষের জীবন চেতনা ও জীবনযাত্রা দ্বান্দ্বিক অসঙ্গতির সমষ্টি মাত্র। তার জৈব স্বভাব তাই কখনো স্বরূপে প্রকাশ পায় না।
এজন্যেই মানুষের চেতনায় কিংবা জীবনাচারে কোনো চরম ও ধ্রুব সত্যের প্রকাশ ও বিকাশ নেই। সব সত্যই সাময়িক। সব শ্ৰেয়োবোধই পারিবেশিক। এরই ফলে মানুষের সাহিত্যে, সমাজে, ধর্মে, আদর্শে, নীতিবোধে, শিল্পকলায় কোনো চিরন্তন ও সর্বমানবিক সত্যের উপলব্ধি ও প্রকাশ নেই। তাই, ধর্ম, সমাজ, আদর্শ, নীতিবোধ, সাহিত্য ও শিল্পকলা স্থানে স্থানে এবং কালে কালে রূপ বদলায়, রঙ বদলায়, বদলায় টঙ, বদলায় ভাষা, বদলায় বক্তব্য।
এ্যডাম-ডেভিড-সলোমনের কালে কিংবা মহাভারতীয় যুগে অথবা গ্রীকপুরাণে নারী সম্বন্ধে চেতনা ছিল একরকম, পরে হয়েছে অন্যরকম। সে-যুগে রাবণেরা সীতা হরণ করেই-হত বীর, পরের যুগে নারীর রূপ-বহ্নিই জ্বালিয়েছে দেবলোক, পুড়িয়েছে সমাজ-সংসার। আজো কুমারীর রূপমুগ্ধতাই প্রেম আর পরস্ত্রীর রূপানুরাগ কাম। তাই বহুপত্নীক রত্নসেনেরা প্রেমিক ও নায়করূপে প্রশংসিত আর আলাউদ্দীন-দেবপালেরা কামুক বলে নিন্দিত। আজকাল বিবাহিত পুরুষের কুমারী রূপানুরাগও কাম বলে ঘৃণিত। রমা-রোহিণী-সাবিত্রীরা যদি হিন্দু না হত, তাহলে তাদের বৈধব্য সমস্যা হয়ে দাঁড়াত না।
তেমনি এককালের গোত্রীয় ঐক্য সংকীর্ণতা ও বর্বরতা বলে গর্হিত হয়ে ধর্মীয় ঐক্যে মহিমা আরোপিত হয়েছে, আবার তা বর্জিত হয়ে সাম্প্রদায়িক ঐক্য হয়েছে কাম্য; তাও নিন্দিত হয়ে দৈশিক-রাষ্ট্রিক ঐক্য হচ্ছে বন্দিত। এর পরে আসবে আন্তর্জাতিক ঐক্যের আহ্বান। এমনি করে জীবন-জীবিকার সবক্ষেত্রেই আসে পরিবর্তন ও বিবর্তন। জীবনের বিকাশ-ধারায় প্রয়োজন। প্রয়াসের সমন্বিত প্রেরণায় রূপান্তর আসছে মনে-মেজাজে। তাই পালটাচ্ছে ভাব, চিন্তা ও কর্ম, বিবর্তিত হচ্ছে আচার ও আচরণ, শিল্প ও সাহিত্য, রুচি ও হিত, নীতি-চেতনা ও জীবনদৃষ্টি।
বৈপরীত্য ও অসঙ্গতি থেকেই বৈচিত্র্যের উদ্ভব। জীবনের ও সমাজের বিচিত্র বিকাশ এতেই হচ্ছে সম্ভব। যারা চিরকালের জন্যে জিয়নকাঠি আবিষ্কারের উৎসুক, তাদের কামনা তাই কখনো পূর্ণ হবে না। ধ্রুবতাকামীরা স্বল্পবুদ্ধি। চলমানতাই জীবন, গতিশীলতাই জিয়নকাঠি। মানুষের বিকাশ-সম্ভাবনা দিগন্তহীন নিঃসীম।
প্রজ্ঞা
শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে সংবাদের সিন্দুক করা নয়, সুন্দর ও সুস্থ জীবন রচনায় প্রবর্তনা দেয়া, সফল সার্থক জীবনযাত্রার পথ ও পাথেয় দান। তেমনি জীবনযাত্রা সুখকর করবার জন্যে প্রয়োজনীয় কৌশল উদ্ভাবনে এবং দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনেই বৈজ্ঞানিক প্রয়াস নিয়োজিত। পার্থিব জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োজন মিটানো ও নিরাপত্তা সাধনই বিজ্ঞানের কর্তব্য। কিন্তু মনোভূমে কল্যাণ-লক্ষ্যে প্রীত, করুণা ও মৈত্রীর চাষ করা এবং ফসল ফলানো হচ্ছে বিবেকী আত্মার দায়িত্ব।
বিজ্ঞানচর্চার মূলে রয়েছে স্বাধীন চিন্তা ও জিজ্ঞাসা। এ অন্বেষা প্রসারিত করে বহির্দষ্টি। এর নাম জ্ঞান। জ্ঞান শক্তি দান করে এবং শক্তি প্রয়োগেই আসে ব্যবহারিক জীবনে সাফল্য ও স্বাচ্ছন্দ্য। যন্ত্রশক্তি তাই আজ অজেয় ও অব্যর্থ। কিন্তু ব্যবহারিক-বৈষয়িক জীবনযাত্রা বাঁচা নয়, বাঁচার উপকরণ মাত্র। কেননা, মানুষ বাঁচে তাঁর আনন্দে ও যন্ত্রণায় অর্থাৎ অনুভবের মধ্যে। সে অনুভবকে সুখকর সম্পদে পরিণত করতে হলে চাই প্রজ্ঞা–যে প্রজ্ঞা কল্যাণ ও সুন্দরকে প্রীতি ও মৈত্রীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা-প্রয়াসী।
বিজ্ঞানের প্রয়োগ-ক্ষেত্রে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার, প্রযোজন ও প্রীতির সমতা রক্ষিত না হলে আজকের মানুষের প্রয়াস ও প্রত্যাশা ব্যর্থতা ও হতাশায় অবসিত হবেই। কেবল তা-ই নয়, প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতিহিংসা জিইয়ে রাখবে দ্বন্দ্ব-সগ্রাম ও সংঘর্ষ-সংঘাত। রাসেল তাই বলেছেন–বিজ্ঞান-লব্ধ শক্তিকে সুপথে চালিত করার সুমতি নেই বলে মানুষ আজ ভয়ঙ্কর বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।
অতএব, আজ যন্ত্রের সঙ্গে জানের, কালের সাথে কলিজার, মেশিনের সাথে মননের, বলের সাথে বিবেকের নিকট ও নিবিড় যোগ থাকা আবশ্যিক। নইলে মানবিক সমস্যা বাড়বে বই কমবে না। মানবকল্যাণে প্রাপ্তির সাথে প্রীতির, জ্ঞানের সাথে প্রজ্ঞার, বিজ্ঞানের সঙ্গে বিবেকের সমন্বয় ও সমতা সাধনই আজকের মানববাদীর গুরু দায়িত্ব ও পবিত্র কর্তব্য।
শিক্ষা
শাস্ত্রের সঙ্গে শিক্ষার বিরোধ ঘুচবার নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য জ্ঞান অর্জন। কেননা জ্ঞানই শক্তি। জ্ঞানমাত্রই বর্ধিষ্ণু। কারণ, জিজ্ঞাসা থেকেই জ্ঞানের উৎপত্তি। জিজ্ঞাসা অশেষ, তা-ই জ্ঞানও কোনো সীমায় অবসিত নয়। বিদ্যা জ্ঞান দেয়। নব নব চিন্তা-ভাবনায় ও আবিক্রিয়ায় জ্ঞানের পরিধি পরিসর কেবলই বাড়ছে। যত জানা যায়, তার চেয়েও বেশি জানবার থাকে। জ্ঞান বৃদ্ধির অনুপাতে তথ্যের স্বরূপ ও তত্ত্বের গভীরতা ধরা পড়ে। এজন্যে জ্ঞানের সাথে ধর্মশাস্ত্র সমতা রক্ষা করতে অসমর্থ।
ধর্মশাস্ত্রীয় সত্য হচ্ছে চিরন্তনতায় ও ধ্রুবতায় অবিচল। তার হ্রাস নেই, বৃদ্ধি নেই, বদল নেই, নেই পরিবর্তন ও পরিমার্জন। পক্ষান্তরে জ্ঞান হচ্ছে প্রবহমান, তার উন্মেষ আছে, বিকাশ আছে, প্রসার আছে, আছে তার বিবর্তন ও রূপান্তর। নতুন তথ্যের উদ্ঘাটন, নব সত্যের আবিষ্কার পুরোনো জ্ঞানকে পরিশোধিত ও পরিবর্তিত করে। যেমন জ্ঞানের ক্ষেত্রে চাঁদ-সূর্য সম্পর্কে তথ্যগত ও তত্ত্বগত সত্যের রূপান্তর ঘটেছে ও ঘটছে এবং জিজ্ঞাসু মানুষ তা দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করেছে ও করছে। কিন্তু শাস্ত্রীয় চাঁদ-সূর্য সম্পর্কে প্রত্যয়জাত সত্যের কোনো পরিবর্তন নেই বেদে-বাইবেলে। জ্ঞানের সাথে বিশ্বাসের বিরোধ এখানেই। জ্ঞান প্রমাণ-নির্ভর আর বিশ্বাস হচ্ছে অনুভূতি-ভিত্তিক। জ্ঞান হচ্ছে ইন্দ্রিয়জ আর বিশ্বাস হচ্ছে মনোজ। চোখ-কানের সাক্ষ্য মানুষ কত সহজেই না অগ্রাহ্য করে! আর মনের দাবী পূরণে কত উৎসুক সে! তার কাছে জ্ঞান অপরিহার্য আর বিশ্বাসই শিরোধার্য। চিত্তলোকে আজো মানুষ জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত এবং বিশ্বাসের অরণ্যে পথের সন্ধানে দিশহারা।
সংস্কৃতির মুকুরে আমরা
পরিশীলিত ও পরিস্রত জীবনচেতনাই সংস্কৃতি। কুসুমের মতো বিকশিত হয়ে উঠে সংস্কৃতিবান মানুষের মন। তার আত্মার লাবণ্য তার আচরণ ও কর্মকে দেয় মাধুর্য। তার কৃতি পরিবেশকে করে স্নিগ্ধ ও সুন্দর। তার মনের রঙে ও প্রীতির সুবাসে জগৎ-সংসারের মানুষ মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত হয়। সংস্কৃতির অপর নাম তাই সৌন্দর্য-অন্বেষা। যা কিছু কুৎসিত ও অসুন্দর তা দেখা, শোনা, বলা ও করা থেকে বিরত থাকাই সংস্কৃতিবানতা। তাই সৌজন্যেই সংস্কৃতির পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠে। জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও কল্যাণবুদ্ধি সংস্কৃতির পরিবর্ধক।
সংস্কৃতি আবার বিদ্যা, জ্ঞান, আর্থিক অবস্থা, মনন-শক্তি ও চারিত্রিক প্রবণতার উপর নির্ভরশীল। তাই একই পরিবারের বা সমাজের কিংবা দেশের লোকের মধ্যেও সংস্কৃতিগত তারতম্য দৃশ্যমান। তাছাড়া সংস্কৃতির জন্ম হয় ব্যক্তিমনে এবং লালন হয় সামাজিক জীবনে। অর্থাৎ একের সৃষ্টি বহুর অনুকরণে ও অনুসরণে দৈশিক ও জাতিক সম্পদ ও ঐতিহ্য হয়ে উঠে।
সংস্কৃতির উৎসও অনেক। কেননা জীবনচেতনা ও জীবনের প্রয়োজন ঋজুও নয়, এককও নয়। এজন্যে ধর্মীয় বিধিনিষেধ, নৈতিক বোধ, আর্থিক অবস্থা, শৈক্ষিক মান, রাজনীতিক প্রজ্ঞা, সামাজিক প্রয়োজন, মানবিক অভিজ্ঞতা, ভৌগোলিক সংস্থান, দার্শনিক চেতনা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি প্রভৃতি অনেক কিছুর সমন্বয়ে গড়ে উঠে এক একটি সংস্কৃতির।
যেহেতু মানুষে মানুষে, চিন্তা, চেতনা ও প্রয়োজনগত ঐক্য রয়েছে, সেহেতু দুনিয়ার সব মানুষেরই ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য দেখা যায়। এবং সংস্কৃতিতে যেহেতু প্রতি মানুষের স্বাভাবিক ও মানবিক প্রয়োজন রয়েছে, অথচ সংস্কৃতি নির্মাণের যোগ্যতা বা প্রতিভা সবার নেই, সেহেতু অপরের অনুকরণে ও অনুসরণেই অর্থাৎ গ্রহণে-বরণেই সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হয়। যারা সৃজন করতে পারে না, এবং গ্রহণও করতে জানে না অর্থাৎ যারা বরণ-বিমুখ, আদিম আরণ্য জীবন তারা আজো অতিক্রম করতে পারেনি। সংস্কৃতি হচ্ছে বহতা নদীর স্রোতের মতো–প্রতি মুহূর্তে নতুন। নিত্য নতুনের সাধনাই সংস্কৃতিবানতা। প্রবাহহীন বদ্ধজল যেমন ক্ষয়িষ্ণু ও আবিলযুক্ত, স্থিতিশীল সংস্কৃতিও তেমনি বিকাশ-বিরহী, কুসংস্কার-প্রবণ, রক্ষণশীল, নতুন-ভীরু ও ক্ষয়শীল।
সুন্দর ও কল্যাণকে যে সহজে গ্রহণ করতে পারে সে-ই সংস্কৃতিবান। দেশ ও কালগত জীবন চেতনা যার সুষ্ঠু সে-ই সংস্কৃতিবান। যে জীবন-চেতনার ও জীবন-প্রতিবেশের বিকাশ ও বিস্তারকামী, যে সমাজবোধকে, নীতিচেতনাকে, ধর্মবুদ্ধিকে এবং আচারনিষ্ঠাকে জীবনের অনুগত করতে জানে, সেই সংস্কৃতিবান।
আমরা বাঙালিরা সৃষ্টি করে ও প্রয়োজনমতো গ্রহণ করেই হয়েছি সংস্কৃতিবান। ধর্মের ক্ষেত্রে আমরা বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য-ইসলাম ও খ্রীস্টধর্ম বাহির থেকেই নিয়েছি। আমাদের শাসন করেছে বিদেশী বিজাতিরা। তাদের থেকেই পেয়েছি প্রশাসনিক ঐতিহ্য। পোশাক-পরিচ্ছদ আসবাবাদিও এসেছে। নানা জাতি থেকে, তা সত্ত্বেও আমরা সবকিছু আমাদের মতো করে নিয়েছি। আমরা ধার করেছি বটে, কিন্তু অনুকরণ করিনি। আমরা বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে এবং ইসলামকেও আমাদের প্রয়োজনসিদ্ধ রূপ দিয়েছি। নিজেরা তার রূপান্তর যেমন ঘটিয়েছি, তেমনি নতুন মতবাদেরও সৃষ্টি করেছি। আমাদের বজ্রযানী-সহজযানী, যোগতান্ত্রিক ও থেরবাদী বৌদ্ধমত, আমাদের লৌকিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম, আমাদের স্বসৃষ্ট দেবতা, অপদেবতা ও উপদেবতা, আমাদের নব স্মৃতি, নব ন্যায়, নব বৈষ্ণববাদ, সহজিয়া বাউলমত, পীরবাদ, ব্রাহ্মমত, ওহাবী-ফরায়েজী-মুহম্মদী মত আমাদের দেশ কালের প্রয়োজন ও যুগ-জীবন চেতনার সাক্ষ্য। আমরা এ জীবনকে, এ জগৎকে সত্য বলে জেনেছি, প্রিয় করে নিয়েছি। তাই এই জীবনের প্রয়োজনকেই মেনেছি। এবং জীবনের অনুগত করে তুলেছি সবকিছুকে। আমাদের ধর্ম, আমাদের নীতিবোধ, আমাদের আচার-আচরণ আমাদের। বিকাশকামী চেতনর রঙে রূপান্তর লাভ করেছে। আমরা জীবনকে চালু আচারের ও বাঁধা নীতির দাস করিনি। রীতি ও নীতিকে চলিষ্ণু জীবনের সহায়ক সহচর করতে চেয়েছি। চিন্তার ক্ষেত্রে আমরা চিরকালই বন্ধন ভীরু বিহঙ্গ। আচারের ক্ষেত্রে অনুগত উদাসীন। তাই ধর্ম-দর্শন ও সাহিত্যাদি শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা নতুনের পিয়াসী ও স্রষ্টা। আচারের ক্ষেত্রে সাহসিক নিরীক্ষাপ্রবণ।
আগেই বলেছি, অনেক ব্যাপারেই মানুষে মানুষে দেশ-কালহীন সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য থাকে। কেননা মানবিক বৃত্তি-প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন মূলত অভিন্ন। তা সত্ত্বেও কোনো দুটো মানুষের সাংস্কৃতিক মান সমান নয়। কারণ কোনো দুটো মানুষের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, সৌন্দর্যবুদ্ধি, কল্যাণবোধ ও আর্থিক অবস্থা অভিন্ন নয়। এ অনেকটা ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্যের বা বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের প্রতিভাস।
তাই ধর্মমতের অভিন্নতা দেশ-কাল নিরপেক্ষ সংস্কৃতির জন্ম দেয় না। যদি তা-ই হত, তাহলে, গোটা দুনিয়ায় কয়েকটা ধর্মীয় সংস্কৃতিই থাকত। কেবল ভাষাই যদি সংস্কৃতির ভিত্তি হত, তাহলে পৃথিবীতে অসংখ্য ভাষাভিত্তিক সংস্কৃতি থাকত। সংস্কৃতি যদি আঞ্চলিক সীমানির্ভর হত, তাহলে ভৌগোলিক সংস্কৃতিই হত সংস্কৃতির উৎস। সংস্কৃতি যদি রাষ্ট্রিক সংস্থাজাত হত, তাহলে রাষ্ট্র ভাঙা গড়ার সঙ্গে সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটত। যদি বিদ্যাই অভিন্ন সংস্কৃতির জনক হত, তাহলে পাশ্চাত্যবিদ্যা এতদিনে সারাবিশ্বের শিক্ষিত সমাজে একটি একক সংস্কৃতি গড়ে তুলত।
অতএব দেশ, কাল, ভাষা, ধর্ম, রাষ্ট্র, কোনটাই এককভাবে সংস্কৃতির জনক নয়, পরিচায়ক নয়, নিয়ামকও নয়। সবকিছুর দানে, প্রভাবে ও মিশ্রণে সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ সম্ভব। কাজেই সংস্কৃতি কখনো অবিমিশ্র হতে পারে না। সৃজনে-গ্রহণে, বরণে-বর্জনে, সংস্কৃতি চিরকাল ঋদ্ধ ও দেশ-কালের উপযোগী হয়েছে।
এজন্যেই কোনো দেশের, সমাজের বা জাতির সংস্কৃতিকে ধর্মের বাঁধনে, সমাজের শাসনে, নীতির নিগড়ে, কালের পরিসরে, দেশের সীমায় রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে অথবা গোত্র বা জাতি-চেতনার অনুগত করে রাখা চলে না।
যে-কোনো মানুষের সংস্কৃতিতে কিছু ধর্মীয় আচারের রঙ, কিছু দেশের জলবায়ুর প্রভাব, কিছু ভাষার রস, কিছু প্রয়োজনের রেশ, কিছু শিক্ষার ফল, কিছু সম্পদের ছাপ, কিছু জ্ঞানের লাবণ্য, কিছু বিদ্যার দান, কিছু হৃদয়বৃত্তির প্রসূন, কিছু মননের মসৃণতা, কিছু প্রজ্ঞার দীপ্তি, কিছু মানবিকতার মাধুর্য, কিছু কল্যাণ-চিন্তার স্নিগ্ধতা থাকেই। সবকিছুর সমন্বয়ে সংস্কৃতি মানুষকে সৃজন করে। তাই সৌজন্যেই সংস্কৃতির পরিচয়। সুজন মাত্রেই মনুষ্যত্বসম্পন্ন। কাজেই সৌজন্যের অপর নাম পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব। অতএব সংস্কৃতি মানবতারই নামান্তর। একজন মনুষ্যত্বসম্পন্ন মানুষই কেবল সুজন ও সুনাগরিক হতে পারে। এমন মানুষ অসত্য, অসুন্দর ও অকল্যাণের শত্রু। একজন জীবনসচেতন সত্যসন্ধ সৌন্দর্যপ্রিয় মানুষ তার মানবিক দায়িত্বে ও কর্তব্যে অবহেলা করে না।
এমন সৌজন্য, দায়িত্বজ্ঞান ও কর্তব্যবুদ্ধি যে-দেশের অধিকাংশ মানুষে সুলভ, সে-দেশের মানুষ সামগ্রিক পরিচয়ে তাই সংস্কৃতিবান বলে অভিহিত হয়। এ অর্থে সংস্কৃতি জীবনবোধের ও জীবনাদর্শের বা জীবননীতির পরিমাপকও। বলেছি, বিশ্ব-মানবের মধ্যে বৈচিত্র্যে ঐক্য এবং ঐক্যে বৈচিত্র্যই সংস্কৃতির সাধারণ লক্ষণ।
আমরা বাঙালিরা অন্তত দু-হাজার বছরের পুরোনো সংস্কৃতিবান জাতি। মানবিক ঐতিহ্য আমরা একদিকে যেমন দেশ-কাল নিরপেক্ষ সংস্কৃতির ধারক, অন্যদিকে তেমনি আঞ্চলিক সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট। এক কথায় আমরা সামান্য ও স্বকীয় সংস্কৃতির ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ। ইতিহাসের সাক্ষ্যে প্রমাণিত যে, আমরা পরধর্ম গ্রহণ করেও তাকে নিজের প্রয়োজনে রূপান্তরিত করে স্বকীয় ও স্বতন্ত্র করে নিয়েছি বারবার। আমরা ধার করেছি কিন্তু অনুকরণ করিনি। বীজ নিয়েছি অন্যের থেকে, কিন্তু স্বকীয় চেতনার, মননের ও আদর্শের পরিচর্যায় আমরা আমাদের মনের মতো ফল ফলিয়েছি। ধর্মে, দর্শনে, ন্যায়ে, আচারে ও চিন্তায় আমরা সত্যকে আবিষ্কার করতে চেয়েছি। সুন্দরের অনুধ্যান ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি, মানবতাকেই মানবধর্ম বলে: স্বীকার করেছি। লোকহিতের অঙ্গীকারে জীবনপ্রয়াস নিয়ন্ত্রিত করতে চেয়েছি। স্বদেশকে, স্বভাষাকে, স্বজাতিকে ও স্বরাষ্ট্রকে ভালোবাসতে শিখেছি। যুদ্ধকে, বিসম্বাদকে, উৎপীড়নকে, স্বার্থপরতাকে ঘৃণা করতে জেনেছি। বিশ্বের পীড়িত-শোষিত মানুষের কান্নায় বিচলিত হয়ে সাড়া দিতে এগিয়ে এসেছি। মনুষ্যত্ব অর্জনে নিষ্ঠা, জীবনে-সমাজে-রাষ্ট্রে সুন্দরের প্রতিষ্ঠা প্রয়াস, মানববাদের জয় কামনা, শান্তির সাধনা, আমাদের সংস্কৃতিকে উজ্জ্বল ও কালানুগ করেছে। আবার আমাদের ভাষার স্বাতন্ত্র, অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, জীবনযাত্রার আঞ্চলিক প্রভাব, উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার অসমতা, ঐতিহ্য ও ইতিহাস আমাদের সংস্কৃতিকে অনন্য স্বাতন্ত্র দিয়েছে।
অতএব সংস্কৃতিতে রয়েছে দ্বৈতাদ্বৈত তত্ত্ব। সংস্কৃতি একাধারে যেমন দেশ-কাল- জাত ধর্ম নিরপেক্ষ (কেননা, সৌন্দর্যে, কল্যাণে ও মানবতায় দেশ-কাল-জাত-ধর্মের পার্থক্য স্বীকৃত নয়, তেমনি দৈশিক-কালিক-জাতিক, ধার্মিক ও বৈষয়িক আভরণও থাকে অবিচ্ছেদ্যরূপে সংস্কৃতিতে লগ্ন। কেননা মানুষের প্রয়াস দেশগত ও প্রয়োজনগত চেতনার অনুগত। কাজেই মানুষের সংস্কৃতি একই লক্ষ্যে অনুশীলিত বলেই তা যেমন সর্বমানবিক; আবার দেশ, কাল ও প্রয়োজনের প্রভাব স্বীকার করে বলে তা তেমনি ব্যক্তিক, সামাজিক, আঞ্চলিক আর ধার্মিকও বটে। সংস্কৃতিতে আমরা তাই বহুতে একের সংহতি, একেতে বহুর বিকাশ লক্ষ্য করি।
পুনরুক্তি দোষ ঘটছে জেনেও বলছি–সৌজন্যেই সংস্কৃতির পরিচয়। মনুষ্যত্বই সংস্কৃতির উৎস ও প্রসূন, বীজ ও ফল। কেননা মনুষ্যত্বই মানুষের সৌন্দর্য-অন্বেষা, কল্যাণ-বুদ্ধি ও মানবপ্রীতি জাগায়। আর কে অস্বীকার করবে যে সৌন্দর্যপ্রিয়তা, কল্যাণকামিতা ও মানবপ্রীতিই সংস্কৃতিবানতার শেষ লক্ষ্য?

