- বইয়ের নামঃ বিশ্বাসঘাতক
- লেখকের নামঃ নারায়ণ সান্যাল
- প্রকাশনাঃ দে’জ পাবলিশিং (ভারত)
- বিভাগসমূহঃ উপন্যাস
০. কৈফিয়ৎ
রচনাকাল : ১৯৭৪
কৈফিয়ৎ
[এই ‘কৈফিয়ৎ’টি আমি গ্রন্থরচনার পরে লিখেছিলাম 13.1.78 তারিখে। ঐতিহাসিক কারণে এটি অপরিবর্তিত আকারে ছাপা গেল। কিন্তু এ-গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ আঠারই মে 1978-এর পরে। ফলে এখন এই ‘কৈফিয়তের একটি কৈফিয়ৎ’ অনিবার্য হয়ে পড়েছে।]
বাঙলা সাহিত্যে সাধারণ-বিজ্ঞান বা পপুলার-সায়েন্স’-এর বই ইদানিং বড় একটা নজরে পড়ছে না। তার পিছনে আছে একটা বিষচক্র। লেখক লেখেন না, কারণ প্রকাশক ছাপেন না, কারণ লাইব্রেরী কেনেন না, কারণ পাঠক পড়েন না! তাছাড়া ইংরেজি ভাষার তুলনায় বাংলা ভাষায় পাঠক-সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য–তাঁদের একটা বিরাট অংশ বিজ্ঞানে উৎসুক নন। ফলে বিজ্ঞানের বই যা লেখা হচ্ছে তা পাঠ্যপুস্তক। না পড়লে পরীক্ষায় পাশ করা যায় না। সাহিত্যের বই অধিকাংশই অবসর বিনোদনের জন্য। যাঁরা এ-দুটি বিষয়কে মেশাতে পারেন তারাও সে চেষ্টা করেন না ঐ বিষচক্রের ভয়ে।
দুটি ব্যতিক্রম বাদে এ-কাহিনির প্রতিটি চরিত্রই বাস্তব। সৌজন্যবোধে যে দুটি নাম আমি পরিবর্তন করেছি তার উল্লেখও ‘পরিশিষ্ট ক’তে দেওয়া হয়েছে, এছাড়া ঘটনার পরিবেশ, কথোপকথন ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রেই আমাকে কল্পনা করে নিতে হয়েছে, কিন্তু বাস্তব তথ্যকে কথাসাহিত্যের খাতিরে কোথাও আমি অতিক্রম করিনি। দশ-বারোটি। স্মৃতিচারণ, জীবনী, বিজ্ঞানগ্রন্থ ও সরকারি রিপোর্ট এ-গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনার মূল উৎস। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতা যতখানি স্বাধীনতা সচরাচর দাবী করে থাকেন আমি বোধহয় ততখানি স্বাধিকারও প্রয়োগ করিনি। তথ্য থেকে যেটুকু বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে তার স্পষ্ট নির্দেশও গ্রন্থশেষে দেওয়া হল।
পাঠকের সুবিধার জন্য দুটি তালিকা আমি যুক্ত করেছি। প্রথমত, গ্রন্থের শেষে একটি কালানুক্রমিক সূচি। কথাসাহিত্যের খাতিরে অনেক সময় অনেক ঘটনা আমাকে। আগে-পিছে বলতে হয়েছে। পাঠকের যাতে কালভ্রান্তি না হয় তাই ওই তালিকাটি। দ্বিতীয় তালিকাটিও গ্রন্থের শেষে দেওয়া হল। তার কৈফিয়ৎ দিই : এ-কাহিনির সব চরিত্রই বিদেশি। বিদেশি নাম যে-বানানে দেওয়া হয়েছে হয়তো স্বদেশে তাদের নাম সে-ভাবে উচ্চারিত হয় না। প্রথমত, অনেক বিদেশি নামের উচ্চারণ বাংলা বর্ণমালাতে প্রকাশই করা যায় না, দ্বিতীয়ত, বিদেশি ভাষা জানা না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে আমাকে আন্দাজে নামগুলি বাংলা হরফে লিখতে হয়েছে। তাই এই তালিকার নামগুলি সাজিয়েছি ইংরাজি বর্ণমালা অনুসারে এবং যে বানানে তারা এখানে উল্লেখিত হয়েছেন, তাও জানিয়েছি। প্রায় আড়াই ডজন নোবেল প্রাইজ প্রাপ্ত চরিত্র এ কাহিনিতে অংশ নিয়েছেন–তাঁদের নামের পাশে তারকাচিহ্ন দেওয়া আছে।
‘পারমাণবিক শক্তি’ ব্যাপারটার সম্বন্ধে আমাদের ভাসা-ভাসা ধারণা আছে। হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে তার নারকীয় কাণ্ডকারখানার কথাও শুনেছি। কিন্তু মোদ্দা ব্যাপারটা যে কী, তা আমরা জানতাম না। জানার প্রয়োজনও এতদিন বোধ করিনি। যা ছিল একান্ত গোপন তার অনেকটাই আজ জনসাধারণকে জানতে দেওয়া হয়েছে। আমেরিকা-রাশিয়া-ব্রিটেন-ফ্রান্স ও চিন-পৃথিবীর পাঁচ-পাঁচটি দেশ এ তথ্য জেনে ফেলেছে, অ্যাটম বোমা ফাটিয়েছে। বিদেশি ভাষায় পপুলার সায়েন্স-জাতীয় বইয়ে এ আলোচনা দেখেছি। বাংলা ভাষায় সে আলোচনা আমার নজরে পড়েনি। গত পঁচিশ-ত্রিশ বছর এ-বিষয়ে অজ্ঞ ছিলাম–তা দুনিয়ার অনেক বৈজ্ঞানিক-তথ্যের বিষয়েই তো কিছু জানি না, কী ক্ষতি হয়েছে তাতে?–ভাবখানা ছিল এই। এতদিনে মনে হচ্ছে–ক্ষতি হয়।
এই কৈফিয়ৎ লিখছি মোমবাতির আলোয়। বিজলি নেই। লোডশেডিং শুধু কলকাতায় নয়, ভারতবর্ষে নয়। পৃথিবী আজ অন্ধকার হতে বসেছে। কয়লার ভাড়ার ক্রমশ বাড়ন্ত হয়ে উঠছে, পেট্রোলের ভাঁড়ে মা ভবানী’-র পদধ্বনি শোনা যায়! কথায় বলে : বসে খেলে কুবেরের ধনও একদিন ফুরোয়! পৃথিবীর অবস্থাও আজ তাই। দুনিয়ার অগ্রসর দেশগুলি তাই আজ শক্তির সন্ধানে ইতি-উতি চাইছে–সূর্যালোকের শক্তি, জোয়ার-ভাটার শক্তি, পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ শক্তি এবং, বিশেষ করে, পারমাণবিক শক্তি।
যুদ্ধোত্তর ইংল্যান্ডে ‘ক্যালডেন হল’ সাফল্যমণ্ডিত হবার পর গ্রেট ব্রিটেন একসঙ্গে অনেকগুলি পারমাণবিক শক্তি-প্রকল্পে হাত দিয়েছিল। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিকরা আশা করেছিলেন–পরের দশকে গ্রেট ব্রিটেনে ব্যবহৃত বিদ্যুৎশক্তির এক-তৃতীয়াংশ এ-ভাবেই পাওয়া যাবে। সে প্রকল্প কতদূর সাফল্যলাভ করেছে তার খবর আর পাইনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 1972 সালে ছয়শত বিলিয়ন ডলারের চেয়েও বেশি খরচ করেছে নূতন শক্তি-উৎসের সন্ধানে। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে 28টি পরমাণু প্রকল্প ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে, 49টিতে কাজ চলছে, আরও 67টি পরিকল্পনার জন্য অর্ডার গিয়েছে। একমাত্র ওক-রিজ প্রকল্পেই পারমাণবিক শক্তির সন্ধানে ব্যয় হবে পঞ্চাশ কোটি ডলার। মার্কিন সরকার আশা রাখেন 1980-র ভেতর যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে ব্যবহৃত বিদ্যুৎশক্তির (3.7 লক্ষ মেগাওয়াট) ত্রিশ-শতাংশ ওরা পারমাণবিক শক্তি থেকে পাবে। কয়লাবিদ্যুতের চেয়ে পরমাণু বিদ্যুতের দামও নাকি পড়বে কম।
রাশিয়া বা চিনের কথা জানি না, কিন্তু যে ভারতবর্ষ জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে বলে স্কুলে থাকতে কোরাস গান গাইতুম তার খবর কী? 1947 এ ক্টর হোমি ভাবার সভাপতিত্বে পরমাণু-শক্তি কমিশনের প্রথম সভা হয়েছিল, তারপর রিসার্চ রিয়্যাকটর ‘অপ্সরা’র উদ্বোধন হল, ‘জারলিনার’র জন্ম হল, রাজস্থানে পরমাণুকেন্দ্র স্থাপনের একটি প্রকল্প শুরু হয়েছে, ট্রম্বেতেও কাজ হচ্ছে বলে জানি। আজকের সংবাদপত্রে নারোয়ায় চতুর্থ পরমাণু কেন্দ্রের শিলান্যাস হবার খবরও ছাপা হয়েছে–কিন্তু আসল কাজ কতদূর হয়েছে জানি না। যেটুকু জানি, তা হচ্ছে এই–মোমবাতির আলোয় এই কৈফিয়ৎ লিখছি!
এটুকু বুঝি যে, আজ যদি আমরা চিত্তরঞ্জনে বিদ্যুৎ-বাহিত রেলওয়ে এঞ্জিনের পরিবর্তে আবার বয়লার এঞ্জিন বানাবার চেষ্টা করি, পেট্রোল, কোলগ্যাস, কয়লা, কেরোসিন, রেড়ির তেল, কাঠ থেকে ধাপে ধাপে নামতে নামতে মা ভগবতীর অকৃপণ দানের ভরসায় বসে থাকি তবে আমাদের নাতি-নাতির’ কপালে দুঃখ আছে।
আজ তাই মনে হচ্ছে, গত পঁচিশ বছরে পারমাণবিক শক্তির বিষয়ে কোনো খোঁজ-খবর না নিয়ে কাজটা ভাল করিনি। আর সেইজন্যই আপনাকে বলব–এ বইটি যদি না পড়েন তো না পড়লেন, কিন্তু আদৌ যদি পড়েন তবে পাতা বাদ দিয়ে পড়বেন না।
আপনার ‘প্রনাতির’ দোহাই!
নারায়ণ সান্যাল
13.1.74
.
আশির দশকের কৈফিয়ৎ
গ্রন্থরচনার দশ বছর পরে এই কৈফিয়ৎটি সংযোজন করা প্রয়োজন বোধ করছি। প্রথম প্রকাশকালেই গ্রন্থটি অধ্যাপক হোমি জাহাঙ্গির ভাবার পুণ্যস্মৃতিতে উৎসর্গীকৃত। দ্বিতীয় কথা, এ গ্রন্থের অটো কার্ল কাল্পনিক চরিত্র। কোনো বাস্তব চরিত্রের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নেই।
আর একটি কথা। বিদেশি নাম এবং বৈজ্ঞানিক শব্দ বাংলা-হরফে প্রকাশ করা খুব কঠিন; যদি লেখকের সেই ভাষাজ্ঞান বা বিশেষ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যথেষ্ট পড়াশুনা না থাকে। ফলে, প্রথম প্রকাশকালে অনেক বিদেশি বৈজ্ঞানিকের নাম আমি বাংলা হরফে ঠিকমতো লিখতে পারিনি। সাহা ইন্সটিট্যুটের অধ্যাপক রাজকুমার মৈত্র, (পি. আর. এস.) ও অধ্যাপক অশোক চট্টোপাধ্যায় এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রঞ্জন ভট্টাচার্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এইজাতীয় ত্রুটির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাকে অসীম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। অনেকগুলি বৈজ্ঞানিক ভ্রান্তিও তাদের কল্যাণে এবারে সংশোধন করা গেল।
নারায়ণ সান্যাল
14.8.84
২. কে?
পনেরই সেপ্টেম্বর 1945।
অর্থাৎ বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে মাত্র একমাস আগে। ইউরেনিয়াম-বোমা-বিধ্বস্ত হিরোশিমা আর প্লুটোনিয়াম-বোমা-বিধস্ত নাগাসাকির ধ্বংসস্তূপ তখনও সরানো যায়নি। জার্মানি, রাশিয়া, ফ্রান্স অথবা জাপানের অধিকাংশ জনপদ মৃত্যুপুরীতে রূপান্তরিত। বিশ্ব এক মহাশ্মশান! মানব সভ্যতার ইতিহাসে এ পৃথিবীতে এতবড় ক্ষয়ক্ষতি আর কখনও হয়নি। সেই মহাশ্মশানে শুধু শোনা যায় মিত্রপক্ষের বিজয়োল্লাসের উৎসব-ধ্বনি–যেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে মাংসভুক শিবাকুলের উচ্ছ্বাস!
প্রিয়-পরিজনদের নিয়ে প্রাতরাশে বসেছিলেন অশীতিপর বৃদ্ধ স্টিমসন। ওয়াশিংটনের অনতিদূরে হাইহোল্ডে, তার বাড়ির ‘ডাইনিং হল’-এ। অশীতিপর ঠিক নন, হেনরি. এল. স্টিমসনের বয়স ঊনআশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবীণ সমরসচিব সেক্রেটারি অফ ওয়্যর। এ বিশ্বযুদ্ধে ছিলেন আমেরিকার সর্বময় কর্তা। প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্টের আমলের লোক–এই বয়সেও অবসর নেননি কর্মজীবন থেকে। নেবার সুযোগও হয়নি। তাকে এতদিন অব্যাহতি দিয়ে উঠতে পারেননি রুজভেল্টের স্থলাভিষিক্ত নতুন প্রেসিডেন্ট-হ্যারি ট্রুম্যান। অন্তত যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত।
তা সেই যুদ্ধ এতদিনে শেষ হল। এবার ছুটি দাবী করতে পারেন বটে স্টিমসন। বিবদমান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র আমেরিকার ভূখণ্ডে কোনো লড়াই হয়নি ক্ষতি হয়েছেপ্রচণ্ড ক্ষতি–আর্থিক এবং জনবলে; কিন্তু আমেরিকার মাটিতে কোনো রক্তপাত ঘটেনি। এজন্য নিশ্চয় অভিনন্দন দাবী করতে পারেন যুদ্ধসচিব। শুধু তাই বা কেন? এ-যুদ্ধের যা চরম ডিভিডেন্ড–আগামী বিশ্বযুদ্ধে তুরুপের টেক্কা-সেটা খেলার শেষে রয়ে গেছে তারই আস্তিনের তলায়! এটা যে কতবড় প্রাপ্তি তা শুধু তিনিই জানেন; আর বোধকরি জানেন–মহাকাল!
হঠাৎ ঝঝন্ করে বেজে উঠল টেলিফোনটা। স্টিমসন মুখ তুলে তাকালেন না। ছুরি-কাটায় যেমন ছিলেন তেমনিই ব্যস্ত রইলেন। টেনে নিলেন জোড়া পোচ-এর প্লেটটা। আবার কোথাও বিজয়োৎসবের আমন্ত্রণ হবে হয়তো! এখন ওই তো দাঁড়িয়েছে একমাত্র কাজ! অর্কেস্ট্রা-নাচ-টোস্ট আর পারস্পরিক পৃষ্ঠ-কণ্ডুয়ন কমপ্লিমেন্টস্ আর কথ্রাচুলেশ। ওঁর নাতনি উঠে গিয়ে টেলিফোনটা ধরল, জানালো গৃহস্বামী প্রাতরাশে ব্যস্ত। পরমূহূর্তেই চমকে উঠল মেয়েটি। টেলিফোনের ‘কথা-মুখে’ হাত চাপা দিয়ে ফিসফিসিয়ে ওঠে : গ্র্যান্ড-পা! ইটস্ ফ্রম হিম্।
হিম! ছুরি-কাঁটা নামিয়ে রাখলেন স্টিমসন। এতে সর্বনামের সার্বজনীন ‘হিম’ নয়, এ আহ্বানে লেগে আছে হোয়াইট-হাউসের হিমশীতল স্পর্শ! টেলিফোনের সঙ্গে যুক্ত ছিল অনেকখানি বৈদ্যুতিক তার–তাই পর্বর্তকেই এগিয়ে আসতে হল মহম্মদের কাছে। যুদ্ধসচিবকে আর উঠে যেতে হল না। ন্যাপকিনে মুখটা মুছে নিয়ে যন্ত্রবিবরে শুধু বললেন : স্টিমসন।
-আপনাকে প্রাতরাশের মাঝখানে বিরক্ত করলাম বলে দুঃখিত। একবার দেখা হওয়া দরকার। আসতে পারবেন?
–শ্যিওর! বলুন কখন আপনার সময় হবে?
–এখনই!
–এখনই! কিন্তু কী ব্যাপার বলুন তো…মানে, এখনই আসছি আমি।
–ধন্যবাদ!-লাইন কেটে দিলেন হ্যারি ট্রুম্যান।
পিতার বয়সী প্রবীণ রাজনীতিককে প্রেসিডেন্ট বরাবরই যথেষ্ট সম্মান দেখিয়ে এসেছেন। তাহলে এভাবে কথার মাঝখানে কেন লাইন কেটে দিলেন উনি? লৌহমানব পোড়খাওয়া স্টিমসন বুঝতে পারেন–ব্যাপারটা জরুরি, অত্যন্ত জরুরি। না হলে এতটা বিচলিত শোনাতো না প্রেসিডেন্টের কণ্ঠস্বর। কিন্তু কী হতে পারে? রণক্লান্ত পৃথিবীতে আজ এখন এমন কী ঘটনা ঘটতে পারে যাতে অ্যাটম-বোমার একচ্ছত্র অধিকারী আমেরিকার প্রেসিডেন্টের গলা কাপবে? কী এমন দুঃসংবাদ আসতে পারে যাতে বিজয়ী যুদ্ধসচিবকে অর্ধভুক্ত প্রাতরাশের টেবিল ছেড়ে উঠে যেতে হয়?
***
সেই পরিচিত কক্ষ। পরিচিত পরিবেশ। সামনের ওই গদি-আঁটা চেয়ারখানায় ট্রুম্যানের পূর্ববর্তী রুজভেল্টকেই শুধু নয়, আরও অনেক অনেককে ওভাবে বসতে দেখেছেন প্রবীণ স্টিমসন–এমনকি প্রথম যৌবনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অন্তে উড়রো উইলসনকেও!
ঘরে তৃতীয় ব্যক্তি নেই। প্রেসিডেন্ট সৌজন্যসূচক সম্ভাষণের ধার দিয়েও গেলেন না। হয়তো প্রভাতটা আজ সু-প্রযুক্ত মনে হয়নি তার কাছে। মনে হল তিনি রীতিমত উত্তেজিত। স্টিমসন তার চেয়ারে ভাল করে গুছিয়ে বসবার আগেই প্রেসিডেন্ট বলে ওঠেন, মিস্টার সেক্রেটারি! আপনি গোয়েন্দা গল্প পড়েন? কোনান ডয়েল, আগাথা ক্রিস্টি?
স্টিমসন নির্বাক!
হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েন ট্রুম্যান। নীরবে পদচারণা শুরু করেন ঘরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে। স্টিমসন যেন পিংপং খেলা দেখছেন। একবার এদিকে ফেরেন, একবার ওদিকে। হঠাৎ পদচারণায় ক্ষান্ত দিয়ে প্রেসিডেন্ট বলে ওঠেন, আজ সকালে কানাডার রাষ্ট্রদূত আমাকে একখানি চিঠি দিয়ে গেছে। প্রাইম মিনিস্টার ম্যাকেঞ্জি কিং-এর ব্যক্তিগত পত্র। আমি…আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি সেখানা পড়ে….
স্তম্ভিত হয়ে গেলেন স্টিমসনও। সম্পূর্ণ অন্য কারণে। তিনি মনে মনে। ভাবছিলেন–হ্যায় ঈশ্বর! স্তালিন নয়, চার্চিল নয়–শেষ পর্যন্ত ম্যাকেঞ্জি কিং! তাতেই এই রণক্লান্ত দুনিয়ার একচ্ছত্র অধীশ্বর হ্যারি ট্রুম্যান এতটা বিচলিত।
প্রেসিডেন্ট নিজ আসনে এসে বসলেন। বললেন, আপনি অবসর চাইছিলেন; কিন্তু এ ব্যাপারটার ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত…।
-কিন্তু ব্যাপারটা কী? কী লিখেছেন প্রাইম মিনিস্টার ম্যাকেঞ্জি কিং?
–একটা গোয়েন্দা গল্প। অসমাপ্ত কাহিনি! এ শতাব্দীর সবচেয়ে রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা কাহিনির প্রথমার্ধ!
সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন মেলোড্রামাটিক লাগল বাস্তববাদী স্টিমসনের কাছে। বললেন, দেখি চিঠিখানা?
ট্রুম্যান টেবিলের উপর থেকে সিলমোহরাঙ্কিত একটি ভারি খাম তুলে নিলেন। বাড়িয়ে ধরলেন স্টিমসনের দিকে। বললেন, ম্যানহাটান-প্রজেক্টের গোপনতম তথ্য ওরা বার করে নিয়ে গেছে!
স্টিমসন স্তম্ভিত! অস্ফুটে বলেন : মানে?
-ইয়েস, মিস্টার সেক্রেটারি! এতক্ষণে মস্কোর বৈজ্ঞানিকেরা তা নিয়ে হাতে-কলমে পরীক্ষা করছেন।
বলিরেখাঙ্কিত উদ্যত হাতটা ধীরে ধীরে নেমে এল স্টিমসনের। একটু ঝুঁকে পড়লেন সামনের দিকে। যেন এইমাত্র একটা 22 মাপের সিসের গোলকে বিদ্ধ হয়েছে বৃদ্ধের পাঁজরা। ককিয়ে ওঠেন তিনিঃ বাটু হাউ অন আর্থ কুড ম্যাকেঞ্জি কিং নো ইট?
ইন্টারকমটাও আর্তনাদ করে উঠল। প্রেসিডেন্টের একান্ত-সচিব নিশ্চয় কোন জরুরি সংবাদ জানাতে চান। কিন্তু ক্ৰক্ষেপ করলেন না ট্রুম্যান। পুনরায় বাড়িয়ে ধরলেন মোটা খামটা। বললেন, এটা পড়লেই বুঝবেন। নিন ধরুন!
আদেশটা বোধহয় কানে যায়নি স্টিমসনের। গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে গেছেন তিনি। কপালে জেগেছে কুঞ্চন। খোলা জানলা দিয়ে দৃষ্টি চলে গেছে বহুদূরে। প্রেসিডেন্ট পুনরায় বলেন : ইয়ে, মিস্টার সেক্রেটারি! দিস্ অসো রিকোয়ার্স এ্যাকশন!
‘অলসো’! অর্থাৎ ইঙ্গিতে প্রেসিডেন্ট বুঝিয়ে দিলেন-এ কোনো যুগান্তকারী উক্তি নয়, ঐতিহাসিক উদ্ধৃতিমাত্র! আর যে-ই ভুলে যাক, যুদ্ধসচিব স্টিমসন ভুলতে পারেন না ওই উদ্ধৃতিটা। ঠিক ওই চেয়ারে বসে আমেরিকার আর এক প্রেসিডেন্ট ঠিক ওই কথা-কটাই বলেছিলেন একদিন। 1939 সালের এগারোই অক্টোবর। সেদিনও মার্কিন প্রেসিডেন্টের হাতে ছিল এমনি একটা ভারি খাম। সেবার সে পত্রখানি এসেছিল লঙ-আইল্যান্ডে পরবাসী শুভ্রকেশ এক বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের কাছ থেকে। স্থান আর কালের পজিটিভ-ক্যাটালিস্ট সেই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকটি সেদিন মার্কিন রাষ্ট্রপ্রধানকে সংকেত পাঠিয়েছিলেন : ‘ইউরেনিয়াম পরমাণুর কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করার মহাসন্ধিক্ষণ সমুপস্থিত। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট সেই চিঠিখানি ঠিক এমন ভঙ্গিতে বাড়িয়ে ধরেছিলেন তার মিলিটারী এ্যাটাশে জেনারেল ‘পা’ ওয়াটসনের দিকে। অতি সংক্ষেপে শুধু বলেছিলেন : পা! দিস্ রিকোয়্যার্স এ্যাকশান।
আজ ছয় বছর পরে সেই ঐতিহাসিক বাক্যটিরই পুনরুক্তি করলেন রুজভেল্টের উত্তরসূরি হ্যারি ট্রুম্যান। তাই ওই ‘অসো। সেবার নির্দেশ ছিল সমুদ্রমন্থনের। সুরাসুরের মন্থনে সমুদ্র মথিত হয়েছিল যথারীতি। তাই আজ আমেরিকা বিশ্বাস। এবার আদেশ হল সেই সমুদ্রমন্থনে উঠে আসা-না অমৃতভাণ্ড নয়, হলাহল-অপহারককে খুঁজে বার করতে হবে।
অশীতিপর রণক্লান্ত যুদ্ধসচিব তার বলিরেখাঙ্কিত হাতটি বাড়িয়ে দিলেন। এবার। গ্রহণ করলেন এই দায়িত্ব।
***
ওইদিনই। ঘণ্টাচারেক পরে। ওয়্যর অফিসের সামনে এসে দাঁড়াল ছোট্ট একটা সিট্রন গাড়ি। পার্কিং জোনে গাড়িটি রেখে শিস দিতে দিতে নেমে আসে তার একক চালক। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের একজন মার্কিন সামরিক অফিসার-কর্নেল প্যাশ। বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চেহারা। সুগঠিত শরীর। দেখলেই মনে হয় জীবনে সাফল্যের সন্ধান সে পেয়েছে এই বয়সেই। তা সে সত্যই পেয়েছে। এফ.বি. আই.-য়ের একজন অতি দক্ষ অফিসার। পদমর্যাদায় প্রথম শ্রেণির নয় তা বলে। কর্নেল প্যাশ ইতিপূর্বে বহুবার এসেছে ওয়্যর অফিসে, যুদ্ধ চলাকালে। নানান ধান্দায়। কিন্তু স্বয়ং যুদ্ধসচিবের কাছ থেকে এমন সরাসরি আহ্বান সে জীবনে কখনও পায়নি। পাওয়ার কথাও নয়। যুদ্ধসচিব এবং কর্নেল প্যাশ-এর মাঝখানে চার-পাঁচটি ধাপ। ওর ‘বস’ কর্নেল ল্যান্সডেলকেই কখনও যুদ্ধসচিবের মুখোমুখি হতে হয়নি। ওয়্যর-সেক্রেটারির অধীনে আছেন চিফ-অফ-স্টাফ জেনারেল জর্জ মার্শাল। প্রয়োজনে বরং তিনিই ডেকে পাঠাতেন এফ. বি. আই.-য়ের প্রধান কর্মকর্তাকে, অর্থাৎ কর্নেল ল্যান্সডেল-এর ‘বস’কে। তার নামটা আজও জানে না প্যাশ। চোখেও দেখেনি কোনোদিন। ঈশ্বরকে যেমন চোখে দেখা যায় না, এক-এক দেশে তার এক-এক অভিধা–এফ. বি. আই.-য়ের প্রধান কর্মকর্তাও যেন অনেকটা সেইরকম। সবাই জানে তিনি আছেন। ব্যস, ওইটুকুই। এভাবেই যুদ্ধমন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষিত হত গোয়েন্দাবাহিনীর। আজ স্বয়ং যুদ্ধসচিবের এডিকং ওকে টেলিফোন করায় তাই একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিল কর্নেল প্যাশ। ব্যস্ত হয়ে বলেছিল, আপনি ঠিক শুনেছেন তো? আমাকেই যেতে বলেছেন? ব্যক্তিগতভাবে?
-হ্যাঁ, আপনাকেই। ঠিক দুটোর সময়।
–যুদ্ধসচিব নিজে ডেকেছেন?
–হ্যাঁ, আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না?
কর্নেল প্যাশ তৎক্ষণাৎ টেলিফোন করেছিল তার উপরওয়ালার কাছে; কিন্তু কর্নেল ল্যান্সডেলকে ধরতে পারেনি তার অফিসে। অগত্যা গাড়িটা বার করে চলে এসেছিল যুদ্ধমন্ত্রকে। দুটো বাজার আর বাকিও ছিল না বিশেষ।
চওড়া সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতেই দেখা হয়ে গেল কর্নেল ল্যান্সডেল-এর সঙ্গে। ধড়ে প্রাণ আসে প্যাশ-এর। বলে, আরে, এই তো আপনি এখানে! আপনার অফিসে ফোন করে
-জানি। রেডিও-টেলিফোনে ওরা আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল।
–কিন্তু কী ব্যাপার? হঠাৎ আপনাকে আর আমাকে—
না! আরও কয়েকজন আসছেন। এবং আসছেন মিস্টার ‘এক্স’!
ফেডারেল ব্যুরো অফ ইন্টেলিজেন্সের সর্বময় অজ্ঞাত বড়কর্তার অভিধা হচ্ছে ‘চিফ’। জনান্তিকে অফিসারেরা বলত মিস্টার ‘এক্স’। সমীকরণের অজ্ঞাত রহস্য!
লিফট বেয়ে উপরে উঠতে উঠতে প্যাশ ভাবছিল–আজ তাহলে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হয়ে যাবে। নামটা না জানা যাক, চাক্ষুষ দেখা যাবে তাকে। কিন্তু ব্যাপারটা কী?
পঞ্চমতলে যুদ্ধসচিবের দফতর। লিফটের খাঁচা থেকে বার হওয়া মাত্র ওদের কাছে এগিয়ে আসে একজন সিকিউরিটি অফিসার। হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে, কর্নেল প্যাশ এবং কর্নেল ল্যান্সডেল নিশ্চয়! আসুন আমার সঙ্গে। এই দিকে।
***
প্রকাণ্ড কনফারেন্স রুম। এ-ঘরে একাধিক যুগান্তকারী অধিবেশন হয়েছে এককালে। টেবিলটায় বিশ-পঁচিশজন অনায়াসে বসতে পারে। বর্তমানে বসেছেন আটজন। কর্নেল প্যাশ ও ল্যান্সডেল, এফ. বি. আই.-য়ের চিফ, যুদ্ধমন্ত্রকের চিফ-অফ-স্টাফ জেনারেল মার্শাল, যুদ্ধনীতি পরিষদের দুজন ধুরন্ধর রাজনীতিক–ভ্যানিভার বুশ এবং জেমস্ কনান্ট। এছাড়া ছিলেন অ্যাটম-বোমা প্রকল্পের সর্বময় সামরিক কর্তা জেনারেল লেসলি গ্রোভস্ এবং ওপেনহাইমার। যুদ্ধ চলাকালে এ প্রকল্পের ছদ্মনাম ছিল : ম্যানহাটান প্রজেক্ট। তার অসামরিক সর্বময় কর্তা ছিলেন মার্কিন বৈজ্ঞানিক ডক্টর রবার্ট ওপেনহাইমার–যুদ্ধান্তে যাঁর নাম হয়েছিল ‘অ্যাটম-বোমার জনক’। জেনারেল গ্রোভসস্ ছিলেন তার সামরিক কর্তা। অ্যাটম-বোমার সাফল্যে এই গ্রোভস্ আর ওপেনহাইমার রাতারাতি জাতীয় বীরে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছেন! সহস্রাধিক বৈজ্ঞানিকের ছ বছরের পরিশ্রমের বৃকোদরভাগ যেন ভাগ করে নিতে চান ওই দুজনে।
কাঁটায় কাঁটায় দুটোর সময় পিছনের দ্বার দিয়ে প্রবেশ করলেন সমরসচিব স্টিমসন। সকলেই উঠে দাঁড়ায়। আসন গ্রহণ করে স্টিমসন সরাসরি কাজের কথায় এলেন : জেন্টলমেন। বুঝতেই পারছেন অত্যন্ত জরুরি একটা প্রয়োজনে আপনাদের এখানে আসতে বলেছি। সমস্যাটা কী এবং কীভাবে তার সমাধান সম্ভব সে কথা আপনাদের এখনই বুঝিয়ে বলবেন এফ. বি. আই. চিফ। আমি শুধু ভূমিকা হিসাবে দু-একটি কথা বলতে চাই। প্রথমেই জানিয়ে রাখছি : আপনাদের সমস্ত সাবধানতা সত্ত্বেও ম্যানহাটান-প্রকল্পের মূল তত্ত্ব রাশিয়ান গুপ্তবাহিনী পাচার করে নিয়ে গিয়েছে! হ্যাঁ, এতক্ষণে মস্কোতে রাশান নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্টের দল হয়তো হাতে-কলমে অ্যাটম-বোমা বানাতে শুরু করেও দিয়েছে!
বৃদ্ধ সমরসচিব থামলেন। প্রয়োজন ছিল। সংবাদটা পরিপাক করতে সময় লাগবে সকলের! কর্নেল প্যাশ-এর মনে পর পর উদয় হল কতকগুলি ভৌগোলিক নাম-ট্রিনিটি : হিরোশিমা : নাগাসাকি–নিউইয়র্ক : শিকাগো : ওয়াশিংটন …
না, না, এসব কী ভাবছে সে পাগলের মতো! সম্বিত ফিরে পেল যুদ্ধসচিবের কণ্ঠস্বরে : হ্যাঁ, এ বিষয়ে আজ আর সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। আজ সকালেই প্রেসিডেন্ট একটি গোপন পত্র পেয়েছেন কানাডা থেকে। চিঠিখানা আমি খুঁটিয়ে পড়েছি। আমাদের এফ. বি. আই. চিফও পড়েছেন। তা থেকে আমাদের দুজনেরই ধারণা হয়েছে বিশ্বাসঘাতক নিঃসন্দেহে একজন বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক! হয়তো নোবেল-লরিয়েট! আমি শুধু বলতে চাই–অপরাধের হিমালয়ান্তিক গুরুত্ব অনুসারে আমরা দয়া করে ছেড়ে কথা বলব না, বলতে পারি না; কিন্তু আপনারা দয়া করে দেখবেন বিশ্ববরেণ্য কোনো বৈজ্ঞানিককে যেন এ নিয়ে অহেতুক লাঞ্ছনা ভোগ করতে না হয়। প্রেসিডেন্টের মত–এবং আমিও তার সঙ্গে একমত–ওই বিশ্বাসঘাতক বৈজ্ঞানিক বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় অপরাধটা করেছে! আমি প্রেসিডেন্টকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি–যেমন করেই হোক, ওই বিশ্বাসঘাতককে আমরা খুঁজে বার করব। আপনাদের কর্মদক্ষতায় আমার অগাধ বিশ্বাস।
এফ.বি. আই.-চিফের দিকে ফিরে এবার বললেন, প্লিজ প্রসীড!
যন্ত্রচালিতের মতো শিরশ্চালন করলেন চিফ। তার এ্যাটাচি-কেস থেকে একটা মোটা খাম বার করে টেবিলের ওপর রাখলেন। বললেন : সংবাদটা আমরা জেনেছি কানাডার প্রধানমন্ত্রী ম্যাকেঞ্জি কিং-এর একটি ব্যক্তিগত পত্র থেকে। তারিখ গতকালের। চিঠিখানা প্রেসিডেন্ট পেয়েছেন আজ সকালে। চিঠির সঙ্গে আছে কানাডা গুপ্তচর বাহিনীর প্রধানের একটি প্রাথমিক রিপোর্ট এবং রাশিয়ান-এম্বাসির খানকয়েক গোপন চিঠির ফটোস্টাট কপি।
শেষোক্ত জিনিসটা হস্তগত হয়েছে এইভাবে : গত ছয়ই সেপ্টেম্বর, অর্থাৎ আজ থেকে মাত্র নয় দিন আগে, অটোয়ায় অবস্থিত রাশিয়ান এম্বাসির একজন কর্মী ঈগর গোজেঙ্কো কানাডা-পুলিসের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চায়। গোজেঙ্কোর বয়স ছাব্বিশ, কানাডায় রাশিয়ান দূতাবাসে সে তিন বছর ধরে কাজ করছে। একটি কানাডিয়ান মেয়েকে সে ভালবাসে এবং তাকে বিবাহ করতে চায়। রাশিয়ান এম্বাসি তাকে সে অনুমতি দেয়নি। গোজেঙ্কো গোপনে মেয়েটিকে বিবাহ করে, তার একটি সন্তানও হয়। খবরটা রাশিয়ান গুপ্তচরবাহিনী জানতে পারে। গোজেঙ্কো মনে করেছিল তার জীবন বিপন্ন। বস্তুত তার ফ্ল্যাটে পাঁচই রাত্রে গুপ্তঘাতক হানা দেয়। কোনক্রমে পালিয়ে এসে গোজেঙ্কো কানাডা-পুলিসের কাছে আশ্রয়ভিক্ষা করে। যেহেতু রাশিয়া আমাদের মিত্রপক্ষ তাই কানাডার পুলিস-প্রধান তাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করেন। মরিয়া হয়ে গোজেঙ্কো সরাসরি ম্যাকেঞ্জি কিং-এর সঙ্গে দেখা করে এবং তার হাতে তুলে দেয় ওই গোপন নথি! এরপর বাধ্য হয়ে তাকে আশ্রয় দেওয়া হয়। ওই গোপন নথিপত্র থেকে জানা যাচ্ছে, রাশিয়ান গুপ্তচর বাহিনী দীর্ঘ তিন চার বছর ধরে এই ফমূলা সংগ্রহের চেষ্টা করেছে এবং অতি সম্প্রতি–গত মাসে–তাদের সে চেষ্টা সাফল্য লাভ করেছে।
রিপোর্ট পড়ে আমি এই কয়টি সিদ্ধান্তে এসেছি :
প্রথমত : অ্যাটম-বোমা তৈরির যাবতীয় তথ্য অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। আকারে সেটি ফুলস্ক্যাপ কাগজের আট পাতা। তাতে একাধিক স্কেচ আঁকা ছিল এবং গাণিতিক অথবা রাসায়নিক সূত্রে ঠাসা ছিল। সমস্ত নথিটাকে মাইক্রোফিলমে সংক্ষিপ্ত করা হয় এবং একটি সিগারেটের প্যাকেটে হস্তান্তরিত করা হয়। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায়, বিশ্বাসঘাতক একজন অতি উচ্চমানের পদার্থবিজ্ঞানী, তিনি সম্পূর্ণ বিষয়টা জেনেছেন, বুঝেছেন এবং সবচেয়ে বড় কথা–তার চুম্বকসার প্রণয়ন করেছেন। আমি এ নিয়ে ডক্টর ওপেনহাইমারের সঙ্গে কথা বলেছি। তার মতে সহস্রাধিক বৈজ্ঞানিকের ছ বছরের সাধনাকে আটখানি পৃষ্ঠায় যিনি সংক্ষেপিত করতে পারেন তিনি একটি দুর্লভ প্রতিভা!
দ্বিতীয়ত : জানা গিয়েছে, বিশ্বাসঘাতক একক প্রচেষ্টায় সবকিছু করেছে। ফলে সে শুধু পরমাণু বিজ্ঞান আর গণিতই নয়, ফটোগ্রাফি এবং মাইক্রোফিলম প্রস্তুতিপর্বও জানে!
তৃতীয়ত : বিশ্বাসঘাতক ইংরাজ অথবা আমেরিকান নয়। তার ছদ্মনাম ছিল ডেক্সটার।
চতুর্থত : মাইক্রোফিলমখানা 11.8.45 তারিখের সন্ধ্যায় হস্তান্তরিত হয়। তারিখটা নিশ্চয়ই মনে আছে আপনাদের। ওইদিন জাপান আত্মসমর্পণ করে। গুপ্তবার্তাটা যে লোক গ্রহণ করে সে হয় আমেরিকান, নয় ইংরেজ। তার ছদ্মনাম ছিল রেমন্ড।
এ-ছাড়া আর কোনো তথ্য এ পর্যন্ত জানা যায়নি। এনি কোয়েশ্চেন?
জেনারেল মার্শাল বললেন, ডেক্সটার যে মার্কিন বা ইংরেজ নয়, এ সিদ্ধান্তে কেমন করে এলেন?
চিফ বললেন, রাশিয়ান এম্বাসিকে ক্রেমলিন নির্দেশ দিচ্ছে, যেহেতু ডেক্সটারের মাতৃভাষা ইংরাজি নয়, তাই সে যেন প্রকাশ্যে রেমন্ডের সঙ্গে বাক্যালাপ না করে। তার উচ্চারণ শুনে লোকে বুঝতে পারবে সে বিদেশি। এ থেকে আমার অনুমান-ডেক্সটারের যেটা মাতৃভাষা, যে ভাষায় সে অনর্গল কথা বলতে পারে, সেটা জানা ছিল না রেমন্ডের।
–আই সী!
উপদেষ্টা-পরিষদের সদস্য জেমস্ কনান্ট এবার প্রশ্ন করেন, জেনারেল গ্রোভসস, আপনি বলতে পারেন ম্যানহাটান প্রজেক্টে যে-কজন বিদেশি বৈজ্ঞানিক কাজ করেছেন তাদের মধ্যে কতজনের পক্ষে এ-কাজ করা সম্ভবপর?
জেনারেল গ্রোভসস্ তৎক্ষণাৎ জবাব দেন, এ প্রশ্নের জবাব আমার চেয়ে ডক্টর ওপেনহাইমারই ভাল দিতে পারবেন–কারণ তিনি ওইসব বৈজ্ঞানিকদের আরও ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন, তাছড়া কাজটা যে কতখানি শক্ত তাও তিনি আমার চেয়ে ভাল বুঝতে পারবেন।
ডক্টর ওপেনহাইমার একটু ইতস্তত করে বলেন, ম্যানহাটান-প্রকল্পে কয়েকশত ওই জাতের বিদেশি কাজ করেছেন; কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কম সংখ্যক পদার্থবিজ্ঞানীকে আমরা প্রতিটি বিভাগে ঢুকবার অনুমতি দিয়েছিলাম। ফলে তারা নিজ নিজ বিভাগের সংবাদই রাখতেন। সব বিভাগের সব কথা জানতে পারেননি। আপনারা জানেন, ম্যানহাটান প্রকল্পের অন্তত দশটি প্রধান শাখা তিন-চার হাজার মাইল দূরত্বে ছড়ানো ছিল। এমন একটি রিপোর্ট তৈরি করতে হলে ওই দশটি কেন্দ্রের অন্তত সাতটির খবর তাকে জানতে হয়েছে–সেই সাতটি কেন্দ্র হচ্ছে–কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, বার্কলে, হানফোর্ড, শিকাগো, ওক রিজ, ডেট্রয়েট এবং লস এ্যালামস। এমন ব্যাপক জ্ঞান সংগ্রহ করতে পেরেছেন মুষ্টিমেয় কয়েকজন মাত্র, ধরুন দশ-পনেরো জন। তার বেশি কখনই নয়।
–আপনি কি দয়া করে সেই দশ-পনেরো জনের নাম আমাদের জানাবেন?
–জানাতে আমার আপত্তি নেই, কিন্তু তার পূর্বে আমি বলে রাখতে চাই কোনো সন্দেহের বশবর্তী হয়ে আমি কিন্তু কারও নাম বলছি না। এঁদের প্রত্যেককেই আমি বৈজ্ঞানিক হিসাবে শ্রদ্ধা করি এবং বিশ্বাসভাজন বলে মনে করি। এটা নিছক ‘অ্যাকাডেমিক ডিস্কাশান’–অর্থাৎ আমি উচ্চারণ করছি সেই কয়েকজন বিদেশি বৈজ্ঞানিকদের নাম, যাঁরা ইচ্ছা করলে এমন একটি গোপন নথি প্রস্তুত করবার ক্ষমতা রাখেন। অর্থাৎ কোন্ কোন্ বিদেশি বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান ওই উচ্চস্তরে পৌঁছাতে পারে–আর কিছু নয়।
–নিশ্চয়। আমরা বুঝেছি, এ কোন অ্যাসপার্শান নয়। বলুন?
-হাঙ্গেরিয়ান পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে আছেন তিনজন–ফন নয়ম্যান, ৎজিলাৰ্ড এবং টেলার, রাশিয়ান দুজন–জর্জ ক্রিস্টিয়াকৌস্কি এবং রোবিনোভিচ, জার্মানির তিনজন- রিচার্ড ফাইনম্যান, হান্স বেথে, এবং জেমস্ ফ্রাঙ্ক। এছাড়া অস্ট্রিয়ান ভিক্টর ওয়াইস্কফ, ইটালির ফের্মি, ব্রিটিশ জেমস চ্যাডউইক এবং ডেনমার্কের নীলস বোহর। এই বারোজন!
বৃদ্ধ স্টিমসন দু-হাতে মাথা রেখে চোখ বুজে বসেছিলেন। তিনি যে ঘুমিয়ে পড়েননি তার প্রমাণ পাওয়া গেল যখন হঠাৎ তিনি আপনমনে বলে ওঠেন, ও গড! হোয়াট এ ম্যাগনিফিসেন্ট লিস্ট টু ফাইন্ড আউট এ ট্রেইটার!
ডক্টর ওপেনহাইমার সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলেন, বেগ য়োর পাৰ্ডন স্যার?
-বলছিলাম কি, ওই বারোজনের কত পার্সেন্ট নোবেল-লরিয়েট?
–প্রায় ফিফটি পার্সেন্ট স্যার! পাঁচজন!
–আপনি তো ওই সঙ্গে প্রফেসর আইনস্টাইনের নামটা করলেন না ডক্টর?
-না। তার কারণ, প্রফেসর আইনস্টাইন কোনদিন ম্যানহাটান-প্রজেক্টের কাঁটাতারের বেড়া পার হননি। না হলে ম্যানহাটান প্রকল্পের চুম্বকতত্ত্ব আটপাতার ভেতর সাজিয়ে দেবার ক্ষমতা আরও অনেকের কাছে। জার্মানির অন্তত পাঁচজন বৈজ্ঞানিক সে ক্ষমতার অধিকারী–প্রফেসর অটো হান, ম্যাক্স বর্ন, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, ওয়াইৎসেকার, অথবা হেইজেনবের্গ। হয়তো জাপানের প্রফেসার নিশিনাও পারেন।
–আই সী! বাই দ্য ওয়ে ডক্টর–এবার যে নামগুলি বললেন তার কত পার্সেন্ট নোক্ল-লরিয়েট?
–এইট্টি পারসেন্ট! এই পাঁচজন জার্মান বৈজ্ঞানিকদের ভিতর চারজনই নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন স্যার।
বৃদ্ধ নিঃশব্দে শুধু মাথা নাড়লেন। আবার চোখ দুটি বুজে গেল তার।
–এনি মোর কোয়েশ্চেন? প্রশ্ন করেন চিফ।
হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় কর্নেল প্যাশ। সর্বকনিষ্ঠ সে-বয়সে এবং পদমর্যাদায়। বলে, মাফ করবেন, কিন্তু রিপোর্টের ওই লাইনটা তো’রেড-হেরিং’ও হতে পারে?
-কোন লাইনটা? আর ‘রেড-হেরিং’ বলতে?
-ওই যে বলা হয়েছে ডেক্সটারের মাতৃভাষা ইংরাজি নয়, ওটা হয়তো ওরা ইচ্ছে করেই লিখেছে। ভেবেছে, যদি কখনও ওই দলিলটা আমাদের হাতে পড়ে তবে আমরা কোনোদিনই আর প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে পাবে না।
কেউ কোনো জবাব দেয় না। এমনটা আদৌ হতে পারে কিনা সবাই তা ভাবছে।
জেনারেল মার্শাল বলেন, এমন কথা হঠাৎ মনে হল কেন তোমার? তুমি কি ওই বারোজনের সঙ্গে কোনো ইংরেজ বা আমেরিকানের নাম যুক্ত করতে চাইছ?
– নো নো স্যার। নট এক্সাক্টলি দ্যাট!–সলজ্জে বলে কর্নেল প্যাশ।
বৃদ্ধ সমরসচিব আবার চোখ খুললেন। বললেন, ইয়ংম্যান, তোমার কথার মধ্যে কিন্তু একটা ইঙ্গিত ছিল! তাছাড়া এই বারোজনের লিস্টটাও কেমন যেন অসম্পূর্ণ মনে হচ্ছে আমার কাছে। বাইবেলের নির্দেশ তা নয়! তুমি আর কিছু বলবে?
দৃঢ়স্বরে মাথা নাড়ে প্যাশ : নো স্যার। আই…আই উইথড্র!
বিড়ম্বনার চূড়ান্ত।
***
ঘর থেকে বেরিয়ে নিচে নেমে এসে কর্নেল ল্যান্সডেল বলে, তুমি বেমক্কা অমন একটা কথা বলে বসলে কেন হে?
পুনরায় লাল হয়ে ওঠে প্যাশ। বলে, কী জানি! ও কথা বলা বোধহয় বোকামিই হয়েছে আমার।
-তা হয়েছে। এসব জায়গায় ভেবেচিন্তে কথা বলতে হয়।
ওরা ধীরপদে এগিয়ে আসে পার্কিং জোন-এর কাছে। প্যাশ গাড়িতে উঠতে যাবে হঠাৎ একটি অফিসার এসে বলে, এক্সকিউজ মি আপনাকে আবার উপরে ডাকছেন।
–কে ডাকছেন?–চমকে ওঠে কর্নেল প্যাশ।
–যুদ্ধসচিব।
ততক্ষণে কর্নেল ল্যান্সডেলও চলে গেছে। এ কী যন্ত্রণা! আবার কেন? বাধ্য হয়ে আবার ফিরে আসতে হল। সেই ঘরেই। ঘর এখন প্রায় শূন্য। বসে আছেন শুধু দুজন। যুদ্ধসচিব স্টিমসন এবং এফ. বি. আই. চিফ! সসম্ভ্রমে অভিবাদন করল কর্নেল প্যাশ।
–টেক ইয়োর সীট প্লিজ–বললেন বৃদ্ধ।
উপবেশন তো নয়, চেয়ারের গর্ভে আত্মসমর্পণ করল প্যাশ।
চিফ বললেন, এবারে বল। হঠাৎ ও কথা মনে হল কেন তোমার?
–আমি…মানে, আমার স্যার ও-কথা বলা বোধহয় ঠিক হয়নি!
–বি ক্যানডিড কর্নেল। ডক্টর ওপেনহাইমার যদি নীলস বোহর, হ্যান্স বেথের নাম বলতে পারেন, তবে তুমিই বা এত ইতস্তত করছ কেন? কোনো ইংরাজি-ভাষীর নাম কি মনে পড়েছিল তোমার?
হঠাৎ পূর্ণদৃষ্টিতে প্যাশ তাকিয়ে দেখল ওই অজ্ঞাতনামা লোকটির দিকে। ওর চিফ-এর দিকে। গম্ভীরভাবে বলল, ইয়েস স্যার।
–কী নাম তার?
–ডক্টর রবার্ট জে. ওপেনহাইমার!
চিফ একবার অপাঙ্গে তাকিয়ে দেখলেন যুদ্ধসচিবের দিকে। বৃদ্ধ নির্বিকার।
-তুমি এবার যেতে পার–বললেন চিফ। ক
র্নেল প্যাশ পুনরায় অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে আসে।
বৃদ্ধ যুদ্ধসচিব এতক্ষণে চিফের দিকে ফিরে বললেন : থ্যাঙ্ক গড! দ্যাট ম্যাড গাই ডিডন্ট মেনশন মাই নেম, অর দ্যাট অফ হ্যারি ট্রুম্যান!
***
পরদিন সকালে জেনারেল গ্রোভসস্ নিজেই এলেন যুদ্ধসচিবের দফতরে। একখানি ফাইল বৃদ্ধের সামনে মেলে ধরে বললেন, পয়েন্টস্ অফ রেফারেন্সগুলি একটু দেখে দিন।
–কিসের পয়েন্টস?
–এ্যাটমিক-এনার্জি এম্পায়োনেজ ব্যাপারে আমরা এফ. বি. আই.কে কোন্ কোন্ বিষয়ে তদন্ত করে দেখতে বলব।
পড়ে যান, শুনি।
–প্রথমত-ম্যানহাটান এঞ্জিনিয়ারিং প্রজেক্ট থেকে আদৌ কোনো গোপন তথ্য বেরিয়ে গেছে কিনা। গিয়ে থাকলে, কতদূর খবর পাচার হয়েছে? দ্বিতীয়ত কে বা কে-কে এই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে? তৃতীয়ত-কানাডার প্রধানমন্ত্রীর পত্রের যাথার্থ্য। চতুর্থত, বিশ্বাসঘাতক কী পরিমাণ উৎকোচ গ্রহণ করেছে? এবং, পঞ্চমত, কোন্ বিদেশি সরকার এই গুপ্তচরবৃত্তিতে উৎসাহ জুগিয়েছে?
–আমার তো মনে হয় ঠিকই আছে।
কাগজখানিতে অনুমোদনসূচক সই করে ফেরত দিলেন যুদ্ধসচিব। তারপর বললেন, বাই দ্য ওয়ে জেনারেল, কাল ওই ম্যাড গাই যে কথাটা বলেছিল সে বিষয়ে আপনার কী ধারণা? কোনো ইংরাজ বা আমেরিকান কি ডেক্সটারের ভূমিকায় নামতে পারে?
–অসম্ভব নয় স্যার। হয়তো সত্যিই ওই লাইনটা একটা ‘রেড-হেরিং। ডেক্সটারের মাতৃভাষা ইংরাজিই–আমাদের বিপথে চালিত করার জন্য ওই পংক্তিটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে লেখা হয়েছে।
তার মানে দাঁড়াচ্ছে–কাল আমরা যে বারোজনের তালিকা নিয়ে আলোচনা করছিলাম আসল অপরাধী তার ভিতর নাও থাকতে পারে?
–ওই অনুমান সত্য হলে তাও সম্ভব স্যার।
-একটা কথা। ম্যানহাটান-প্রজেক্টে যেসব প্রথম শ্রেণির অসামরিক বৈজ্ঞানিকদের নিযুক্ত করা হয়েছিল, তাদের নিয়োগের পূর্বে প্রতিটি ক্ষেত্রেই তো এফ. বি. আই.-কে দিয়ে সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স করানো হয়েছে?
–নিশ্চয়!
–ওই বারোজনের মধ্যে এমন কেউ কি আছেন যাঁর ক্লিয়ারেন্স দিতে এফ. বি. আই. আপত্তি জানায়?
–না। আমি কাল রাত্রেই অফিসে ফিরে ওই বারোজনের ব্যক্তিগত ফাইল খুঁটিয়ে দেখেছি। প্রত্যেকেরই সিকিউরিটি-ক্লিয়ারেন্স আছে।
-ধন্যবাদ!
জেনারেল গ্রোভসস্ কাগজপত্র গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে আসছিলেন। হঠাৎ কী মনে করে থেমে পড়েন। বলেন, একটা কথা স্যার। কথাটা স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই এ-সময়ে বলে রাখতে চাই, যদিও আপনি এ প্রশ্ন করেননি
-ইয়েস জেনারেল?
–ওই বারোজনের ক্লিয়ারেন্স সম্বন্ধে আপত্তিকর কিছু না থাকলেও তার বাইরে একজন টপ-র্যাঙ্কিং বৈজ্ঞানিক আছেন, যিনি প্রতিটি প্রজেক্টের ভিতরে গিয়েছেন এবং গোপনতম সংবাদ জেনেছেন–যাঁর ক্লিয়ারেন্স এফ. বি. আই. দেয়নি
-ইস ইট? কার কথা বলছেন আপনি?
–ডক্টর আর. জে. ওপেনহাইমার!
বৃদ্ধের ভ্রূযুগলে ফুটে উঠল কুঞ্চন। কাঁচের কাগজচাপাটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, স্ট্রেঞ্জ! এফ. বি. আই.-য়ের ক্লিয়ারেন্স ছাড়া কেমন করে তাকে ওই সর্বোচ্চ পদে বসানো হল?
-এফ. বি. আই. য়ের ক্লিয়ারেন্স ছাড়াই তাকে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছিল। যিনি দেন, তিনি ওই বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। প্লেনিপোটেনশিয়াল মিলিটারি অথরিটি।
–আই সী! তিনি কে, জানতে পারি?
–আমি নিজেই স্যার!
–হু!
বৃদ্ধ আবার চুপ করে যান। জেনারেল গ্রোভসস নীরবে অপেক্ষা করেন। বৃদ্ধ পুনরায় বলেন, সেক্ষেত্রে দয়া করে একবার ডক্টর ওপেনহাইমারের পার্সোনাল ফাইলটা আমাকে পাঠিয়ে দেবেন?
নিশ্চয়ই দেব, স্যার!
বিদায় নিয়ে চলে আসছিলেন জেনারেল গ্রোভসস, হঠাৎ পিছন থেকে তাকে আবার ডাকলেন যুদ্ধসচিব : আই সে জেনারেল, অমার মনে হয় পয়েন্টস্ অফ রেফারেন্সের ওই চার-নম্বর আইটেমটা নিষ্প্রয়োজন। ওটা আমাদের জানা আছে।
চমকে ওঠেন গ্রোভস। বলেন, বিশ্বাসঘাতক কী পরিমাণ অর্থ উৎকোচ হিসাবে, পেয়েছিল তা আপনার জানা আছে স্যার?
–আই থিংক সো। একটু অঙ্ক কষতে হবে। ত্রিশ ‘ডুকাট’ উনিশ শ’ বছর ফিক্সড ডিপোজিটে রাখলে সুদে-আসলে কত রুবত্স হয় সেটা হিসাব করে বার। করা শক্ত নয়! বারোজন নয়, এখন তো আমরা তেরোজনের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করছি!
জেনারেল গ্রোভসসও খ্রিস্টান, কিন্তু তিনি নিতান্তই সামরিক অফিসার। এ উক্তির তাৎপর্য ধরতে পারেন না। বৃদ্ধ কিন্তু ততক্ষণে কাগজপত্রের মধ্যে ডুবে গিয়েছেন।
৩. কী ১-৫
০১.
পাঠক আমাকে মাফ করবেন। এ পর্যন্ত পড়ে যদি আপনার ধারণা হয়ে থাকে যে, আমি একটি জবর গোয়েন্দা-কাহিনি কেঁদে ফেলেছি, তাহলে আমি নাচার। আজ্ঞে না! এটি আদৌ গোয়েন্দা-গল্প নয়। এ-কাহিনির আদ্যন্ত বাস্তব। যে বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক ওই গোপন তথ্য রাশিয়ায় পাচার করে দেন তার নাম, ধাম, তার বিচারের বিবরণ ইত্যাদি একদিন ও-সব দেশে সাড়ম্বরে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল। হয়তো আপনাদেরও নজরে পড়েছে তা। অপরাধীটির পরিচয় যখন আগেভাবেই সবাই জেনে বসে আছেন তখন এটা গোয়েন্দা-গল্প হবে কোন হিসাবে?
হ্যারি ট্রুমানের সঙ্গে আমি একমত : মানব সভ্যতার ইতিহাসে এতবড় গুপ্তচরবৃত্তির নজির আর নেই। কিন্তু তাই বলে প্রবীণ যুদ্ধসচিবের সঙ্গে আমি আদৌ একমত নই–এই গুপ্তচরবৃত্তির আর্থিক মূল্যমান দু-হাজার বছরে সুদে-আসলে ‘ত্রিশ ডুকাট যত রুবলস’ হয় ততখানি মোটেই নয়। অনেক আঁকজোক করে আমি যে ইকোয়েশানটা পেয়েছি তা x(x—10^9) = 0! সুধীজনমাত্রেই বুঝবেন তার অর্থ হতে পারে দু-জাতের– কোয়াড্রাটিক ইকোয়েশানটার দুটো ‘রূট’। এক হিসাবে এ গুপ্তচরবৃত্তির আর্থিক মূল্যমান = বিলিয়ন ডলার! টেন-দু দি পাওয়ার নাইন ডলার্স! প্রায় সাড়ে সাত হাজার কোটি টাকা!
দ্বিতীয় হিসাবে এর মূল্যবান স্রেফ : শূন্য!
আপনি কোন্ অঙ্কফলটা মেনে নেন তা আমি সকৌতুকে লক্ষ্য করব।
প্রথমে বলি–ওই বিলিয়ন ডলারের হিসাবটা কেমন করে পেলাম।
সে হিসাবটা বুঝতে হলে প্রথমেই জানতে হবে ‘অ্যাটম’ বা পরমাণু জিনিসটা কী। তার পরের ধাপ–সেই পরমাণু থেকে কেমন করে পারমাণবিক বোমা’ বানানো হল। সে প্রায় অর্ধশতাব্দীর ইতিহাস।
গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাস থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় তেইশ শতাব্দী ধরে পণ্ডিতদের ধারণা ছিল, প্রতিটি মৌল পদার্থের পরমাণু নিরেট, অবিভাজ্য এবং অপরিবর্তনশীল। যে-কোনো মৌল পদার্থের–ধরা যাক লোহা কিম্বা সোনাকে যদি আমরা টুকরো টুকরো করতে থাকি তবে এমন একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পর্যায়ে পৌঁছাব-বাস্তবে নয়, মানসিক ধারণায়–যখন তাকে আর ভাঙা যাবে না। সেটাই হচ্ছে লোহা বা সোনার পরমাণু–সেটা অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু নিরেট, একটা মার্বেলের গুলির মত–তাতে আছে ওই লোহা বা সোনার মৌল ধর্ম।
পরমাণু যে নিরেট নয় এ-কথার প্রথম ইঙ্গিত দিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি (1897) ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক স্যার জে. জে. টমসন (1856-1940)। কেমব্রিজের ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে তিনি বললেন যে, পরমাণু নিরেট নয়, তার ভিতর অন্তত দুটি অংশ আছে। মাঝখানে আছে কেন্দ্রস্থল বা নিউক্লিয়াস এবং বাইরের দিকে ঘূর্ণমান কিছু ইলেকট্রন। তাঁর শিষ্যস্থানীয় লর্ড রাদারফোর্ড (1871-1932) ওই একই ল্যাবরেটরিতে আবিষ্কার করলেন (199) কেন্দ্রস্থলের ‘প্রোটন এবং তার চোদ্দ বছর পরে (1932) রাদারফোর্ড-এরই শিষ্য জেমস্ চ্যাডউইক (1891-1974) একই গবেষণাগারে আবিষ্কার করলেন ‘নিউট্রন’। দিনেমার পণ্ডিত নীলস বোহর (1885-1962) বিভিন্ন পরমাণুর রূপরেখার সম্বন্ধে ধারণা দিলেন। এসব কথা আমরা পরে ধাপে ধাপে আবার আলোচনা করব। এখন মোদ্দা কথাটা বলে নিই, যাতে পরমাণুর আকৃতি সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা করে নিতে পারি। যদিও সঠিক ধারণা করা অসম্ভব!
বিজ্ঞানীরা বললেন, পরমাণুর গঠন কেমন জানো? অনেকটা এই আমাদের সৌরজগতের মতো। মাঝখানে আছে সূর্যের প্রতীক পরমাণু নিউক্লিয়াস। তার দুটি অংশ। ধনাত্মক বিদ্যুৎবহ প্রোটন আর বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ নিউট্রন। গ্রহের মতো ইলেকট্রনগুলি ঋণাত্মক বিদ্যুৎ নিয়ে ওই কেন্দ্রস্থলের চারিদিকে ক্রমাগত পাক খাচ্ছে। ওঁরা আরও বললেন, প্রতিটি প্রোটনের ধনাত্মক বিদ্যুতের পরিমাণ প্রতিটি ইলেকট্রনের ঋণাত্মক বিদ্যুতের সমান। ফলে প্রতিটি পরমাণুতে প্রোটন আর ইলেকট্রন থাকবে সমান সংখ্যায়। ঘরে যতগুলি প্রোটন, বাইরে ততগুলি ইলেকট্রন। যেহেতু নিউট্রনে কোনো বিদ্যুৎ নেই তার সংখ্যা যতই হোক না কেন গোটা পরমাণুটা হচ্ছে ইলেকট্রোনিউট্রাল, অর্থাৎ বিদ্যুতের বিচারে নিরপেক্ষ। প্রতিটি মৌল পদার্থে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রোটন থাকবে–যেমন হাইড্রোজেন-এ একটি, হিলিয়ামে দুটি, কার্বনে ছয়টি, অক্সিজেন-এ আটটি–এভাবে বাড়তে বাড়তে সবচেয়ে ভারী মৌলপদার্থ ইউরেনিয়ামে 92টি। বলা বাহুল্য ওই ওই পরমাণুতে ওই ওই সংখ্যক ইলেকট্রনও থাকবে।
নিউট্রন কোথায় কত থাকবে তারও মোটামুটি নির্দেশ আছে; কিন্তু সে সংখ্যাটা সামান্য এদিক-ওদিকও হতে পারে। নাইট্রোজেনে আটটি নিউট্রনও থাকতে পারে আবার পাঁচটিও থাকতে পারে। ওরা দুজনেই নাইট্রোজেন–প্রথমটি কুলীন নাইট্রোজেন, দ্বিতীয়টি তার জ্ঞাতিভাই–নৈকষ্য-কুলীন নয়, তার আইসোটোপ। অনুরূপভাবে ইউরেনিয়ামে 92টি প্রোটন এবং 92টি ইলেকট্রন আছে, কিন্তু নিউট্রন কখনও থাকে 143টি, কখনও 146টি। নিউট্রন আর পোটন-সংখ্যাকে যোগ করে তাই একটাকে বলি ইউ-235 অপরটাকে ইউ-238। ওরা দুজনেই ইউরেনিয়ামের জ্ঞাতিভাই বা আইসোটোপ।
বেশ কথা, পরমাণু না হয় নিরেট নাই হল –সেটা অবিভাজ্য আর অপরিবর্তনশীল তো বটে? এ-বিষয়েও প্রথম খটকা লাগল 1919 সালে, রাদারফোর্ডের একটি পরীক্ষায়। কেমব্রিজের ওই ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরিতেই উনি পরীক্ষা করছিলেন। একটা কাঁচের নলে নাইট্রোজেন গ্যাস ভরে তার উপর উনি দ্রুতগামী আলফা-পার্টিক-এর আঘাত হানছিলেন।
কিন্তু তাহলে এবার বলতে হয়, আলফা-পার্টিকল্স কাকে বলে?
টমসন-সাহেবের ইলেকট্রন আবিষ্কারের (1897) বছর দুই আগে (1895) জার্মানিতে রনৎজেনসাহেব (1845-1923) এক্স-রে আবিষ্কার করে বসলেন নিতান্ত দৈবক্রমে। সে গল্পটা অনেকেরই জানা। কাঁচের টিউবের ভিতর বিদ্যুৎ-প্রবাহের পরীক্ষা করছিলেন তিনি। হঠাৎ নজরে পড়ে, কালো কাগজে-মোড়ানো কিছু ফটোগ্রাফিক প্লেটে কুয়াশার মতো ছোপ পড়েছে। ব্যাপার কী! উনি বুঝলেন, এমন এক অদ্ভুত রশ্মির সন্ধান উনি পেয়েছেন যার ভেদশক্তি সাধারণ আলোকরশ্মির চেয়ে বেশি। উনি তার নাম দিলেন–অজ্ঞাত-রশ্মি বা ‘এক্স-রে’। সেই ‘এক্স-রে’ আজ কীভাবে কাজে লাগে তা সকলেরই জানা।
***
রনৎজেন-সাহেবের ওই আবিষ্কারের বছরখানেক পরে (1896) ফরাসি বৈজ্ঞানিক বেকরেল (1820-1891) ওই-জাতের একটি পরীক্ষা করেছিলেন। উনি পরীক্ষা করেছিলেন ‘গুরুতম’ মৌল পদার্থ ইউরেনিয়াম নিয়ে। উনি দেখলেন, সূর্যালোকে ওই ইউরেনিয়াম টুকরো থেকে অদ্ভুত একজাতের রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। উনি প্রথমে ভেবেছিলেন এ-বুঝি এক্স-রেরই কাণ্ডকারখানা। কিন্তু পরে দেখলেন, বিদ্যুৎ-প্রবাহ বন্ধ থাকলেও এবং সূর্যালোক ব্যতিরেকেও রশ্মি বিচ্ছুরিত হচ্ছে ওই ইউরেনিয়াম থেকে। এটা যে কেন হচ্ছে তা ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি তিনি। এই রশ্মি-বিকিরণের নাম দেওয়া হল ‘রেডিয়েশান’।
এ-সম্বন্ধে গবেষণা করে জগৎ-বিখ্যাত হলেন কুরি-দম্পতি। ফরাসি বৈজ্ঞানিক পিয়ের কুরি (1859-1006) আর তাঁর স্ত্রী মাদাম কুরি (1867-1934)। পিয়ের ছিলেন পারি বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। মারি কুরির আদি নিবাস পোল্যান্ডে–ফ্রান্সে এসেছিলেন ডিগ্রি নিতে। সেখানেই উভয়ের পরিচয়, প্রণয় ও পরিণয়। ওঁরা দুজনে এক টন মতো আকরিক ইউরেনিয়াম নিয়ে পরীক্ষা করেছিলেন; কিন্তু একটা জিনিস কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না। এক টন আকরিক ইউরেনিয়ামে কতটা ইউরেনিয়াম আছে তা ওঁদের জানা। সে-হিসাবে রেডিয়েশানের পরিমাণ কতটা হওয়া উচিত তাও হিসাব কষে বার করেছেন। অথচ দেখা যাচ্ছে বাস্তবে রেডিয়েশানের পরিমাণ অনেক, অনেক বেশি। ওঁদের ধারণা হল ওই আকরিক ইউরেনিয়াম-নমুনায় ইউরেনিয়াম ছাড়া আরও কোনো অজ্ঞাত মৌল পদার্থ আছে, যার রেডিয়েশানের পরিমাণ আরও বেশি। এভাবে খুঁজতে খুঁজতে ওঁরা আবিষ্কার করলেন ‘রেডিয়াম। শুধু রেডিয়াম নয়, আরও অনেকগুলি ‘রেডিও-অ্যাকটিভ’ মৌল পদার্থ আবিষ্কৃত হল, যেমন পোলোনিয়াম, রেডন, থোরিয়াম ইত্যাদি।
***
কিন্তু এই রেডিও-অ্যাকটিভিটি ব্যাপারটা কী? সেটা নিয়ে গবেষণা করতে বসলেন কেমব্রিজ বিজ্ঞানাগারের প্রফেসর আর্নেস্ট রাদারফোর্ড। আদি বাড়ি নিউজিল্যান্ডে। কেমব্রিজে এসেছিলেন গবেষণা করতে। উনি দেখলেন, বাইরের কোনো কারণ ছাড়াই কোনো অজ্ঞাত আভ্যন্তরিক তাগিদে রেডিও-অ্যাকটিভ মৌল-পদার্থগুলি ক্রমাগত শক্তি বিকিরণ করে চলেছে। শুধু তাই নয়, শক্তি বিকিরণ করতে করতে আপনা-আপনি তারা রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। ধরুন রেডিয়াম। রেডিয়ামের পারমাণবিক ওজন 226। অর্থাৎ হাইড্রোজেন-পরমাণুর তুলনায় সেটা 226 গুণ ভারী। এই রেডিয়াম শক্তি বিকিরণ করতে করতে ক্রমশ পরিণত হচ্ছে রেডন-এ, যার পারমাণবিক ওজন 222। সেখানেই থামছে না কিন্তু। যে-হেতু ‘রেডন’ নিজেও রেডিও-অ্যাকটিভ, তাই তা থেকে জন্ম নিচ্ছে আরও হালকা কোনো বস্তু। এভাবে শেষ পর্যন্ত এসে থামছে ‘লেড’-এ, অর্থাৎ সীসায়, যার পারমাণবিক ওজন হচ্ছে 205। প্রতিটি রেডিওঅ্যাটিভ মৌল পদার্থের এই আত্মক্ষয়ী ধর্মের গচ্ছিন্দও পরিমাপ করা গেল। রেডিয়াম এভাবে শক্তিক্ষয় করতে করতে 1,600 বছরে অর্ধপরিমাণ হয়ে যায়, 3,200 বছরে সিকি-পরিমাণ। ইউরেনিয়ামের রেডিও- অ্যাকটিভিটি কম–অন্তত চার শ’ কোটি বছর তার লেগে যাবে অর্ধেক হতে।
এটা মেনে নেওয়া রীতিমত কষ্টকর হয়ে পড়ল বিজ্ঞানীদের কাছে। এতদিন জানা ছিল প্রতিটি পরমাণু অপরবির্তনশীল এবং বাইরের কোনো কারণ আরোপিত না হলে কোনো কার্য’ হয় না। অথচ দেখা যাচ্ছে, ইউরেনিয়াম আপনা থেকেই হয়ে যাচ্ছে রেডিয়াম, রেডিয়াম হচ্ছে রেডন–এভাবে পরিবর্তিত হতে হতে সব কয়টি রেডিও-অ্যাটিভ পদার্থ এসে থামছে সীসায়! কারণটা কী?
রাদারফোর্ড ওই রেডিও-অ্যাকটিভিটি ধর্মটার বিশ্লেষণ করতে বসলেন। সীসার একটি পাত্রে তিনি সামান্য একটু রেডিয়াম রেখে দিলেন এবং পাত্রের একদিকে ঋণাত্মক অপরদিকে ধনাত্মক বিদ্যুৎবাহী তারের প্রান্ত এনে রাখলেন। দেখলেন, রেডিয়াম-টুকরো থেকে তিন জাতের শক্তি বিকিরিত হচ্ছে। একদল রশ্মি বেঁকে যাচ্ছে ঋণাত্মক বিদ্যুতের দিকে, তাকে বললেন আলফা-পার্টিকলস। একদল রশ্মি বাঁক নিচ্ছে ধনাত্মক বিদ্যুতের দিকে, তার নাম দিলেন বিটা পার্টিকলস্। তৃতীয় দল না ডাইনে না বাঁয়ে কোনো দিকে না বেঁকে সিধে উঠে যাচ্ছে উপর দিকে। তার নাম দিলেন গামা-রশ্মি। (চিত্র 1)
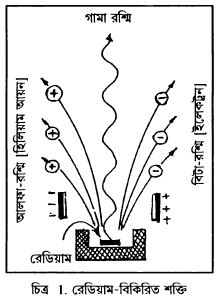
[চিত্র 1. রেডিয়াম-বিকিরিত শক্তি]
উনি প্রমাণ করলেন, এই গামা-রশ্মি হচ্ছে একজাতের ‘ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ’ বা তড়িৎ-চৌম্বকীয় তরঙ্গ। অত্যন্ত শক্তিশালী–অনেকটা এক্স-রে ধর্মী, যদিও তরঙ্গভঙ্গ আরও ছোট। বিটা-রশ্মি বস্তুত ঋণাত্মক ইলেকট্রন এবং আলফা-রশ্মি হচ্ছে ধনাত্মক বিদ্যুত্বহ হিলিয়াম কেন্দ্রক। একটি হিলিয়াম আয়নের পারমাণবিক ওজন হচ্ছে চার, তাই রেডিয়াম (226) থেকে একটি হিলিয়াম কেন্দ্রক (4) বিচ্ছুরিত হওয়া মাত্র তা রূপান্তরিত হচ্ছে রেডন-এ (226-4 = 222)।
এরপর রাদারফোর্ড পরমাণুর অন্তরে কী আছে তা জানবার জন্য সচেষ্ট হলেন। অর্থাৎ আমরা তাঁর সেই 1919 সালের যুগান্তকারী পরীক্ষার প্রসঙ্গে ফিরে এসেছি। মনে রাখতে হবে, এই পরীক্ষার সময় রাদারফোর্ড পরমাণুর আকৃতি-প্রকৃতির কথা কিছুই জানতেন না। ইলেকট্রন তার পূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু পোটন, নিউট্রন, সৌরজগতের মতো পরমাণুর আকৃতি ইত্যাদি কিছুই তার জানা ছিল না।
রাদারফোর্ড জানতে চাইলেন, পরমাণুর ভিতরে কী আছে? কেমন করে জানবেন? জানার সবচেয়ে ভাল উপায় তার অন্তরে আঘাত করে দেখা। তোমার মনে কী আছে জানতে হলে আমাকে আঘাত করতে হবে তোমার অন্তরে, দেখতে হবে কোন্ আঘাতে তুমি কী ভাবে সাড়া দাও। কী দিয়ে আঘাত করবেন? কেন, সদ্য-আবিষ্কৃত ওই আলফা-পার্টিক বা হিলিয়াম কেন্দ্ৰক দিয়ে করা যেতে পারে।
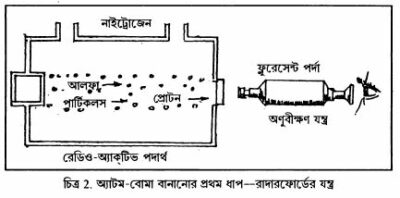
[চিত্র 2. অ্যাটম-বোমা বানানোর প্রথম ধাপ—রাদারফোর্ডের যন্ত্র]
এগুলি প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন। আলোর গতির শতভাগ থেকে দশভাগের মধ্যে। অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে 3,000 কিলোমিটার থেকে 30,000 কি. মি.। রেডিয়াম থেকে বিচ্ছুরিত এই দ্রুতগতি রশ্মি দিয়ে তিনি নাইট্রোজেন গ্যাসের পরমাণুতে আঘাত করতে চাইলেন। যে যন্ত্রে তিনি এ পরীক্ষাটা করেছিলেন সেটি সযত্নে আজও রাখা আছে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছোট্ট যন্ত্র। দেখতে চিত্র 2-এর মতো। কাঁচের টিউবটার ভেতরে আছে শুধু নাইট্রোজেন গ্যাস। যন্ত্রের বাঁ দিকে রেডিও-অ্যাটিভ উৎস থেকে যে আলফা পার্টিকলস্ বিচ্ছুরিত হচ্ছে তা 15 সেন্টিমিটার দূরত্বে যেতে পারে না। অথচ উনি ডানদিকের অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখলেন, রেসেন্ট পর্দাটা আলোকিত হচ্ছে। রাদারফোর্ড বললেন, তার কারণটা হচ্ছে এই যে, দ্রুতগামী আলফা-পার্টিকলগুলি টিউবের ভিতরে অবস্থিত নাইট্রোজেন পরমাণুর অন্তর বিদীর্ণ করেছে। নাইট্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রস্থিত কোনো ধনাত্মক-বিদ্যুৎগর্ভ অংশ বিমুক্ত হয়েছে। উনি তার নাম দিলেন প্রোটন। অর্থাৎ তার হিসাব মতো দাঁড়ালো পরমাণুতে আছে দুটি অংশ : কেন্দ্রস্থলে ধনাত্মক বিদ্যুৎগর্ভ প্রোটন এবং তার বাইরে টমসন-সাহেব-বর্ণিত চক্রবর্তনকারী ইলেকট্রন। রাদারফোর্ড তার এ পরীক্ষায় ওই দুটি অংশকে পৃথক করেছেন। অর্থাৎ পরমাণুর অন্তর বিদীর্ণ হয়েছে। বস্তুতপক্ষে পরমাণু-রাজ্যে সেই হল প্রথম বিপ্লব।
অ্যাটম-বোমা বানানোর সর্বপ্রথম ধাপ!
***
তখন কিন্তু সে-কথা কেউ কল্পনাই করেনি। তাই এ আবিষ্কার গোপন করার কথা কারও মনেও আসেনি। প্রফেসর রাদারফোর্ড তৎক্ষণাৎ তার পরীক্ষার ফলাফল ছাপিয়ে ফেললেন। বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়ে তা ছাপা হল বিভিন্ন দেশে-জার্মানিতে, ফ্রান্সে, রাশিয়ায়, জাপানে।
বিজ্ঞানের কাঁধে তখনও রাজনীতির জোয়াল চাপেনি। বিজ্ঞানের নাকে রাষ্ট্রনায়কেরা তখনও দড়ি পরায়নি। বিশ্ববিজ্ঞানের দ্বার তখন ছিল উন্মুক্ত, অবারিত।
কিন্তু একটা কথা। পরীক্ষান্তে রাদারফোর্ড দেখলেন-তার যন্ত্রের ভেতর যা পড়ে আছে তা অধিকাংশই অক্সিজেন! নাইট্রোজেন নয়! এমনটা কী করে হল তার ব্যাখ্যা উনি সে সময়ে দিতে পারেননি।
রাদারফোর্ড এই পরীক্ষাটা করেছিলেন 1919-এর শেষাশেষি। অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (1914-1918) শেষে। পরীক্ষায় যখন তন্ময় হয়ে আছেন–যুদ্ধ তখনো চলছে–তখন ওঁর এক সহকারী এসে মনে করিয়ে দেয়,-স্যার! যুদ্ধমন্ত্রকে একটা জরুরী অধিবেশনে আজ আপনার যাওয়ার কথা–
ওঁর ওই ছয় ইঞ্চি (15 সেমি) লম্বা যন্ত্রের উপর ঝুঁকে পড়ে তখন বুঁদ হয়ে আছেন সাতচল্লিশ বছর বয়সের আর্নেস্ট রাদারফোর্ড। বাঁ-হাতটা তুলে শুধু বললেন, গোল কোরো না–
মারণাস্ত্র বিষয়ে যুদ্ধমন্ত্রকে বিজ্ঞানীদের কনফারেন্স। যুদ্ধ-সচিব, প্রধান সেনাপতি সবাই থাকবেন। সেখানে অনুপস্থিত থাকা মানে একটা যুদ্ধাপরাধ! আধঘণ্টা পরে সহকারীটি আবার মনে করিয়ে দেয়,-স্যার! এখানে অক্সিজেন কোথা থেকে এল সেটা কাল দেখলে হয় না?
যন্ত্রে-নিবদ্ধদৃষ্টি রাদারফোর্ড একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা শুধু বলেছিলেন, মাই বয়! মাই নেম ইজ ‘আর্নেস্ট’!
জরুরি মিটিং-এ অনুপস্থিত তালিকায় লেখা হল একটি নাম–ডক্টর আর্নেস্ট রাদারফোর্ড।
যুদ্ধমন্ত্রীর বিশেষ সংবাদবহ পরদিন কেমব্রিজে এসে হানা দিল। বেশ কড়া মেজাজে কৈফিয়ৎ তলব করল রাদারফোর্ড-এর। তখনও তিনি ব্যারন হননি–লর্ড রাদারফোর্ড নন, প্রফেসর রাদারফোর্ড। সামরিক অফিসারটিকে রাদারফোর্ড নাকি বলেছিলেন, আস্তে কথা বলুন মশাই! আমি এখন একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করছি!
আরও বলেছিলেন, আমার এ পরীক্ষা ইঙ্গিত দিচ্ছে পরমাণুকে বিভক্ত করা সম্ভব। তার অর্থ আপনার মাথায় ঢুকবে না, আপনার বড়কর্তাকে শুধু বলবেন–আমার অনুমান সত্য হলে এই ল্যাবরেটরির ভেতর আজ যেটা ঘটছে তা একটা বিশ্বযুদ্ধ জয়ের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিছু বুঝলেন?
নিঃসন্দেহে নিরেট ধাতুর হেলমেট ভেদ করে সামরিক অফিসারটির মস্তিষ্কে ব্যাপারটা ঢোকেনি। তা না ঢুকুক–কেমব্রিজ ক্যাভেন্ডিশ-ল্যাবরেটরিতে ঢুকলে আজও দেখতে পাবেন টাঙানো আছে একটি নোটিস : টক সফটলি প্লীজ!
‘আস্তে কথা বলুন, মশাই!’
পরের বছর, জুন মাসে ‘ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে’ প্রকাশিত হল রাদারফোর্ড-এর প্রবন্ধ। একটা নতুন দিগন্ত দেখা দিল। প্রমাণিত হল–যুগযুগান্ত ধরে মানুষ যা কল্পনা করে এসেছে, সেই আদিম অ্যালকেমিস্টরা যে স্বপ্ন দেখেছেন, তা নিতান্ত গাঁজাখুরি না-ও হতে পারে। লোহাকে সোনা নয়, রাদারফোর্ড নাইট্রোজেনকে রূপান্তরিত করেছেন অক্সিজেন-এ! কী করে করেছেন তা অবশ্য বোঝা গেল না। কিন্তু করেছেন।
***
আরও একটা প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল না। কারণ ছাড়া কার্য হয় না-যন্ত্রী ছাড়া যন্ত্র বাজে না। রেডিয়াম কিছু ভগবান নয় যে, আপসে-আপ তেজ বিকিরণ করবে! রসায়ন এ সমস্যার সমাধান করতে না পারলেও পদার্থবিদ্যার এক পণ্ডিত তা করলেন। তিনি সর্বযুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইন (1879 1955)। 26, বছর বয়সে (1905) তিনি বললেন, পদার্থের ‘ভর’ আর ‘শক্তি’ দুটি বিচ্ছিন্ন ধারণা নয়, তারা বাগর্থের মতো সম্পৃক্ততাদের একটি যোগসূত্র আছে। শক্তি পদার্থকে জন্ম দিতে পারে, আবার পদার্থের বিলোপেও জন্ম নেবে শক্তি। সেই যোগসূত্রটি পাওয়া যাবে যে ফর্মুলায় সেটি হল E =mc2। এত ছোট ফর্মুলায় এতবড় বিপ্লবাত্মক কথা আর কোনো বৈজ্ঞানিক মানব সভ্যতার ইতিহাসে কখনও বলেননি! উনি যেন বলতে চাইলেন : “শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি ‘যম্নোক্তং’ গ্রন্থকোটিভিঃ”। সেই শ্লোকটি হচ্ছে E = mc2; এখানে E হচ্ছে এনার্জি বা শক্তি, m হচ্ছে বস্তুর ‘ম্যাস’ বা ভর আর c হচ্ছে আলোর গতিবেগ, অর্থাৎ প্রতি সেকেন্ডে 300,000 কিমি। উনি বললেন, বস্তুর ভর’ও এক ধরনের শক্তিই’! হিসাব কষে দেখালেন, এক গ্রাম পরিমাণের কোনো মৌল পদার্থ যদি সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ করে, তবে তা থেকে জন্ম নেবে যে শক্তি তার পরিমাণ চার হাজার টন কয়লা জ্বালালে যতটা উত্তাপ পাওয়া যাবে ততটা! তাই রেডিয়াম যখন নিজে থেকেই আত্মবিলোপ ঘটাচ্ছে তখন সে শক্তির জন্ম দিচ্ছে। যেহেতু আত্মবিলোপের গতিটা অতি ধীরে (রেডিয়ামের ক্ষেত্রে 1,600 বছরে অর্ধেক) তাই যে-কোনো খণ্ড-মুহূর্তে যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি পাওয়া যাচ্ছে না। যদি কোনো কৃত্রিম উপায়ে অল্প সময়ে কোনো পদার্থ আত্মবিলোপ করে তবে তা প্রচণ্ড শক্তির জন্ম দেবে। এ-কথাটাতেও আশঙ্কা করার কিছু ছিল না তখন–কারণ কৃত্রিম উপায়ে পদার্থের আত্মবিলোপ ত্বরান্বিত করার কথা তখন কেউ চিন্তাই করতে পারেনি।
প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে একটা কথা এখানে বলে নিই। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় যেসব মনীষীর অবদান আজ স্বীকৃত তার মধ্যে আছেন একজন ভারতীয়বস্তুত বাঙালি– বৈজ্ঞানিক। তিনি আমাদের জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু (1894 – 1974)। ম্যাক্সওয়েল ও বোলম্যানের একটি বৈজ্ঞানিক সূত্রের তিনি নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, যার নাম হয়েছিল বোস-আইনস্টাইন সংখ্যায়ন’। এখন অবশ্য তার নাম শুধু ‘বসু-সংখ্যায়ন’। 1924 সালে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার। ম্যাক্স প্লাঙ্ক-এর কোয়ান্টাম থিওরির এই ব্যাখ্যা তিনি তৈরি করেন এবং একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে আলবার্ট আইনস্টাইনকে সেটি জানান। আইনস্টাইন তার মূল্য অনুধাবন করে তাকে প্রথম স্বীকৃতি দেন। প্রবন্ধটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে Zeitschrift fur Physik পত্রিকায় প্রকাশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানী মহলে সত্যেন্দ্রনাথের আসন প্রতিষ্ঠিত হল। উত্তরকালে অনুরূপ চিন্তধারা নিয়ে কাজ করে গিয়েছেন পাওলি, (1900-1958), এনরিকো ফের্মি (1901-1954) প্রভৃতি। বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন যে, বিশ্বের মৌলিক কণাগুলি-দু-জাতের। ফোটন, মেসন, গ্রাভিটন প্রভৃতি কণা,–যারা বোস-স্ট্যাটিসটিক্স মেনে চলে তাদের নামকরণ করা হল ‘বোসনস’। আর ইলেকট্রন, মিউওন, মেস, নিউক্লিয়ন, বগরায়ন কণা–যারা ফের্মির সংখ্যায়ন মেনে–চলে তাদের নাম হল ‘ফের্মিয়নস’। সত্যেন্দ্রনাথ শাশ্বতকাল ভারতবর্ষের জাতীয় অধ্যাপক থাকবেন না–কিন্তু তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় ‘বসু-সংখ্যায়ন’ আর ‘বোসনস’ মহাকালের দরবারে চিরন্তন-সনদ পেয়ে স্থায়ী আসন গেড়েছে।
.
০২.
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (1914-1918) শেষে ইউরোপ-খণ্ডে, বস্তুত পৃথিবীতেই, ছিল তিনটি মূল ঘাঁটি–যেখানে ‘পরমাণু-তত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা হচ্ছিল। একটি কেন্দ্র ছিল–আগেই বলেছি–কেমব্রিজে। প্রফেসর রাদারফোর্ড ছিলেন তার অধিকারী-মশাই। আর মূলগায়েন তার দুই সাকরেদ–ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক জেমস চ্যাডউইক (1891-1974) আর রাশিয়ান বিজ্ঞানী পিতর কাপিৎজা (1894 – 1984)। চ্যাডউইক সম্মানের সর্বোচ্চ-শিখরে উঠেছিলেন, কাপিৎজাও তাই উঠেছিলেন, কিন্তু রাশিয়ায়। আমরা প্রথমদিকে তাঁর কীর্তিকাহিনির কথা জানতে পারিনি। তিনি নোবেল-পুরস্কার পাওয়ার (1978) পর জানা গেল রাশিয়ায় এতদিন তিনি কী কাজ করছিলেন। দ্বিতীয় কেন্দ্র ছিল ডেনমার্ক-এ। সেখানে দীপ্ত সূর্য নীলস বোহর! ঋষিপ্রতিম বিজ্ঞানভিক্ষু। যেন মাটির দুনিয়ার মানুষ নন, হ্যান্স অ্যান্ডারসনের উপকথালোকের বাসিন্দা! বয়সে রাদারফোর্ডের চেয়ে চৌদ্দ বছরের এবং আইনস্টাইনের চেয়ে ছয় বছরের ছোট; কিন্তু বিজ্ঞানচর্চায় সমান উৎসাহী। কোপেনহেগেন-এ ছিল তার বিজ্ঞানমন্দির। আর তিন নম্বর কেন্দ্রটি ছিল খাস জার্মানিতে। বার্লিন এবং বিশেষ করে গোটিনজেন বিশ্ববিদ্যলয়ে। এখানে সূর্য-টুর্য নেই–জ্যোতিষ্কের ছড়াছড়ি! গোটা গ্যালাটিক সিস্টেম! ম্যাক্স বর্ন, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, জেমস্ ফ্রাঙ্ক, ডেভিড হিলবার্ট, ওয়াল্টার নেস্ট,–কিছু পরে অটো হান, ওয়াইৎসেকার, হেইজেনবের্গ! কাকে ছেড়ে কার কথা বলি?
ওই গোটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়টাকে আর একটু কাছে গিয়ে দেখা যাক বরং। এ শতাব্দীর আদি ও মধ্যযুগে, বিশেষ করে পরমাণু বোমার বিবর্তনে এই গোটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অসামান্য ভূমিকা আছে। বার্লিন থেকে ফ্রাঙ্কফুর্ট যাওয়ার পথে ঘনসন্নিবদ্ধ পপলার, বার্চ আর এম-এর ছায়াঘেরা ছোট্ট একটি জনপদ–সেখানে কারখানা নেই, হৈ-হল্লা নেই, রাজনৈতিক বক্তৃতামঞ্চ নেই, –আছে একটি বিশ্ববিদ্যালয়। যেন গুপ্তযুগে পাটলিপুত্র থেকে রাজগৃহে যাবার পথে শান্ত জনপদ-নালন্দা! অথবা বলতে পারেন, ত্রিশ-চল্লিশের দশকে কলকাতা-সিউড়ি যাবার পথে–শান্তিনিকেতন!
বিশ্ববিজ্ঞানের ইতিহাসে ওই অনাড়ম্বর বিশ্ববিদ্যালয়টির একক দান অসামান্য। দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, জীববিদ্যা, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার দিকপাল পণ্ডিতেরা এখান থেকেই জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকরশ্মি বিকিরণ করেছেন। তবু গোটিনজেন-এর খ্যাতি অঙ্কশাস্ত্র বিষয়েই। গত শতাব্দীতে কার্ল গাউস্ এবং ফেলিক্স ক্লীন ছিলেন এই জ্যোতির্ময়লোকের যুগ্মতারকা। এ-নালন্দার যুগ্ম-শীলভদ্র, অথবা এ-শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র-অবনীন্দ্র! আমরা যে-সময়ের কথা বলছি তখন গোটিনজেন-এ তিন-তিনজন দিকপাল মনীষী ছিলেন এ-রাজ্যের ত্রিরত্ন। তারা হলেন ডেভিড হিলবার্ট (1862-1943), ম্যাক্স বর্ন (1882-1970) আর জেমস্ ফ্রাঙ্ক (1882-1964)। শেষোক্ত দুজনেই ইহুদি এবং নোবেল-লরিয়েট। হিলবার্ট ছিলেন বিশুদ্ধ গণিতের পণ্ডিত-অঙ্কশাস্ত্র ছাড়া এ দুনিয়ায় আর কিছু চিনতেন না তিনি। অপরপক্ষে ম্যাক্স বর্ন এর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। প্রায় লেঅনার্দোর মত। চিত্রশিল্প আর বেহালা বাজানোতে তার এমন পারদর্শিতা ছিল যে, বিজ্ঞান-চর্চা আদৌ না করে ওই দুটি পথের যে কোনো একটায় সিধে হাঁটা ধরলেও তিনি নাকি বিশ্ববিশ্রুত হতে পারতেন। বাবা ছিলেন সম্ভ্রান্ত পরিবারের একজন ইহুদি। পুত্রকে কলেজে পাঠাবার সময় বলেছিলেন, কী নিয়ে জীবন কাটাবে তা স্থির করার আগে সবকয়টি পাঠ্যবিষয়কেই যাচাই করে দেখে নিও। পিতৃ-আজ্ঞা বর্ণে বর্ণে পালন করেছিলেন ম্যাক্স বর্ন। আইন, সাহিত্য, মনস্তত্ত্ব, রাজনৈতিক-অর্থনীতি এবং জ্যোতির্বিদ্যা–পরপর অনেকগুলি বিষয়েই পরীক্ষা দিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত কোনো বিষয়েই দ্বিতীয় হতে পারলেন না। ফলে তিনি পিতাকে লিখে পাঠালেন : সব কয়টি বিষয়ই যাচাই করে দেখলাম। স্থির করেছি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের সামগ্রিক চর্চা করব অতঃপর! এমন মানুষকে পদার্থবিজ্ঞানীরূপে চিহ্নিত করা যায় কিনা জানি না; কিন্তু সেটাই তার পরিচয়।
জেমস্ ফ্রাঙ্কও ইহুদি। হামবুর্গে বাড়ি। অভিজাত পরিবারের সন্তান। আর সেই আভিজাত্য ছিল তার রক্তে। কখনও কারও কাছে মাথা নত করেননি। ছাত্রদের তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, ছাত্রেরাও তার জন্য প্রাণপাত করতে প্রস্তুত। গোটিনজেন-এ আসবার পরেই তিনি কতকগুলি যুগান্তকারী আবিষ্কার করে বসলেন, যার একটির জন্য তাকে যেতে হল সুইডেনে–নোবেল প্রাইজ আনতে।
প্রতি বছরই বিভিন্ন দেশ থেকে বিজ্ঞানীরা আসেন গোটিনজেন-এ-দেখতে, শুনতে জানতে এবং জানাতে। কোয়ান্টাম-থিওরির জনক ম্যাক্স প্লাঙ্ক (1858 – 1947), রেডিয়াম আবিষ্কারক মাদাম কুরি, আপেক্ষিকতাবাদী আইনস্টাইন, পোটন-উদ্ধারক রাদারফোর্ড, পরমাণু-সিদ্ধান্ত-বাচস্পতি নীলস বোহর প্রভৃতি এসেছেন বারে বারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা অধিকাংশই ছাত্রাবাসে থাকত না। তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত সারা শহরে। স্থানীয় বাসিন্দাদের পেইং-গেস্ট হিসাবে, একটি দুটি করে। তার ফলশ্রুতিটি মারাত্মক এবং কৌতুকবহ! বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এক ধুরন্ধর সংখ্যাতত্ত্ববিদ কাগজে ছাপিয়ে দিলেন এক মারাত্মক স্ট্যাটিসটিক্স : সারা পৃথিবীর প্রথমশ্রেণির বিজ্ঞানীদের অধিকাংশের শ্বশুরবাড়ি নাকি ওই ছোট্ট জনপদ গোটিনজেনে! হাটে হাঁড়ি ভাঙা হল আর কি! বোঝা গেল পেইং-গেস্টের দল শুধুমাত্র বিজ্ঞানচর্চাই করেননি এতকাল।
***
জার্মানির চতুর্দিকে কলকারখানা, কর্মব্যস্ততা–অথচ ওই শান্ত ছায়াঘেরা। জনপদে যারা বাস করে তারা যেন গ্রহান্তরের মানুষ। সে-আমলের একজন গোটিনজেন-ছাত্রের স্মৃতিচারণ থেকে কিছুটা উদ্ধৃতি দেবার লোভ সামলাতে পারছি না :
“মাঝে মাঝে মনে হত আমার আশেপাশের মানুষগুলো বুঝি পাগলাগারদের বাসিন্দা! একদিন, মনে আছে, সাইকেল চেপে কলেজ থেকে ফিরছি। এক বৃদ্ধ আমার চাকার তলায় পড়েন আর কি! কোনোক্রমে ব্রেক কষে আমি নেমে পড়ি। বেশ বাগিয়ে একটা ধমক দিতে যাব, দেখি তার আগেই বৃদ্ধ হুমড়ি খেয়ে পড়লেন একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে। ধরে তুলতে গেলাম। আয় বা! প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বসলেন আমাকে : আমি আছাড় খাই না খাই, তাতে তোমার কী হে ছোকরা? দিলে তো সব ভেস্তে?”
“কী ভেস্তে দিলাম আমি? পরে শুনেছিলাম তিনি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। পথে চলতে চলতে মনে মনে আঁক কষতেন। আমি তাকে ধরে তুলতে যাওয়ায় তার নাকি চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল!
“কলেজের পাশেই ছিল ক্যান্টিন। সেখানে কফি-সেবনের অনুপান ‘স্ন্যাকস নয়, ‘সামস’! সাদা মার্বেল-টপ টেবিলে হাতির শুড়ের মতো অদ্ভুতদর্শন লম্বা টান দিয়ে পেনসিলে আঁক কষতেন অধ্যাপক আর ছাত্রের দল। ক্যান্টিনের ম্যানেজারের উপর কর্তৃপক্ষের কড়া হুকুম ছিল–অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত লেখাগুলো যেন না মুছে ফেলা হয়। কখনও কখনও মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কফি-বার খুলে রাখতে হত ম্যানেজারকে। বসে বসে হাই তুলত। আঁক শেষ হয়নি, এই অজুহাতে। আবার এমনও হয়েছে পরদিন এসে দেখা গেছে ইতিমধ্যে কোনো অজ্ঞাতনামা কফি-সেবী অসমাপ্ত অঙ্কের বাকি কটা ধাপ লিখে রেখে গেছেন।
“সে এক অদ্ভুত জগৎ!”
এইযুগে গোটিনজেন-এর ছাত্র ছিলেন এমন কয়েকজন ভবিষ্য-বিজ্ঞানী যাঁরা ওই পরমাণু-বোমা নির্মাণে নানাভাবে অংশ নিয়েছেন। কেউ প্রত্যক্ষভাবে, কেউ পরোক্ষভাবে–আবার কেউ কেউ সেই কালিদাসের ধাঁধার ছন্দে : ‘নেই তাই খাচ্ছ, থাকলে কোথায় পেতে!’–অর্থাৎ তারা পরমাণু-বোমা নির্মাণে কোনো অংশ না নিয়েই এ নাটকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ। মার্কিন মুলুকের ওপেনহাইমার (1904-1967), ইটালির এনরিকো ফের্মি, রাশিয়ার জর্জ গ্যামো (1904-1968), হাঙ্গেরির ৎজিলাৰ্ড (1898-1964) আর টেলার (1908 ) নিয়েছিলেন প্রত্যক্ষ ভূমিকা। আর কালিদাসী ধাঁধার ছন্দে অংশ নিয়েছিলেন জার্মানির হেইজেনবের্গ (1901-1976), ওয়াইৎসেকার (1912- ), ভন লে, অটো হান (1879-1968) প্রভৃতি–অ্যাটম-বোমা না বানিয়ে। কেন? তা যথাসময়ে বলব।
শেষোক্ত দলের মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠ এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় ছিলেন নোবেল-লরিয়েট অটো হান। হেইজেনবের্গ তার ছাত্রস্থানীয়, বয়সে অনেক ছোটো। অদ্ভুত প্রতিভাশালী। জীবনে কখনও কোনো প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হননি। মাত্র তেইশ বছর বয়সে তিনি প্রফেসার নীলস বোহর-এর প্রধান শিষ্য হয়ে পড়েন, চব্বিশ বছর বয়সে কোপেনহেগেন-এ অধ্যাপনা শুরু করেন এবং ছাব্বিশে লিপজিগে পুরোপুরি পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদ অলঙ্কৃত করেন। মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে তিনি নোবেল-প্রাইজ পেয়েছিলেন–শুধু তাই নয়, যে আবিষ্কারের জন্য এ-পুরস্কার তাকে দেওয়া হয় সেটা তিনি সম্পন্ন করেছিলেন তার পঁচিশ বছর বয়সে! যখন অধিকাংশ বিজ্ঞানী ডক্টরেটও করে উঠতে পারেন না।
***
এই নিরুদ্বিগ্ন শান্ত-জনপদে ধূমকেতুর ধূসর ছায়াপাত ঘটল উনিশ শ তিরিশ-বত্রিশে। জার্মানির ভাগ্যাকাশে দেখা দিল ন্যাশনাল সোসালিস্ট দল–যার কর্ণধার নাকি কে এক অজ্ঞাতকুলশীল অ্যাডলফ হিটলার (1889-1945)। বছর না ঘুরতেই শোনা গেল ন্যাশনাল সোসালিস্ট দলের নাম হয়েছে নাৎসি পার্টি, তারা জার্মানির শাসনযন্ত্র দখল করেছে (1933)। হিটলার হয়েছে জার্মানির ভাগ্যবিধাতা। ওই সঙ্গে শোনা গেল একটা অদ্ভুত কথা : জার্মানির সব সমস্যার মূলে নাকি আছে ইহুদি-সম্প্রদায়। শুরু হয়ে গেল ইহুদি-বিতাড়ন পর্ব, জার্মানি থেকে। বার্লিনে এক বিজ্ঞান-পরিষদের বক্তৃতামঞ্চ থেকে নামিয়ে দেওয়া হল আলবার্ট আইনস্টাইনকে। হিটলারের স্নেহধন্য একদল পণ্ডিতম্মন্য বললে–আইনস্টাইনের ওই আপেক্ষিকতাবাদ আসলে একটা ইহুদি ধাপ্পাবাজি।
হিটলারের ক্ষমতা দখলের মাসখানেকের ভিতরেই গোটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে উপস্থিত হল একটি মারাত্মক টেলিগ্রাম। সাত-সাতজন প্রথম শ্রেণির অধ্যাপককে পদচ্যুত করা হয়েছে। অপরাধ–তারা ইহুদি। সেই সাতজনের একজন হচ্ছেন ম্যাক্স বর্ন। ইংল্যান্ডে চলে গেলেন তিনি।
প্রথমটা স্তম্ভিত হয়ে গেল গোটিনজেন। তারপর শুরু হল আবেদন-নিবেদন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ইহুদি অধ্যাপকদের চলে যেতে হল। বাইশজন প্রথিতযশা আর্য-বিজ্ঞানী একবার শেষ চেষ্টা করলেন গণ-দরখাস্ত পাঠিয়ে–তার ভিতর ছিলেন আধ-ডজন নোবেল লরিয়েট। হিটলারের দপ্তরে পৌঁছে সেটা সোজাসুজি চলে গেল ছেঁড়া-কাগজ-ফেলার ঝুড়িতে।
প্রথম শ্রেণির ইহুদি অধ্যাপকদের মধ্যে একমাত্র রেহাই দেওয়া হল জেমস ফ্রাঙ্ককে। বোধকরি তিনি কয়েক বছর আগে (1925) নোবেল প্রাইজ পাওয়ায়। কিন্তু আভিজাত্যের মর্যাদায় অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক হিটলারের এ দাক্ষিণ্য গ্রহণ করলেন না। পদত্যাগ করলেন তিনি–কারণটা স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে : যেহেতু বর্তমান সরকার জার্মান-ইহুদিদের দেশের শত্রু হিসাবে গণ্য করেছেন তাই তিনি অব্যাহতি চান।
তৎক্ষণাৎ গৃহীত হল ফ্রাঙ্কের পদত্যাগপত্র। শুধু তাই নয়, ওই বিজ্ঞান-জ্যোতিষ্কের বিদায়ে যাতে কোনো সভার আয়োজন না করা হয় সে বিষয়েও কড়া নির্দেশ এল। স্ত্রীর হাত ধরে নীরবে বিদায় হলেন তিনি গোটিনজেন থেকে। এমনকি নোবেল-প্রাইজের মেডেলটাও নিয়ে যেতে পারেননি।
গোটিনজেন-এর ত্রিরত্নের দুজন বিতাড়িত। শেষ দীপশিখাঁটি জ্বালিয়ে রেখেছেন একা ডেভিড হিলবার্ট–গণিত-সাগর। তিনি পুরোপুরি নর্ডিক–ইহুদি রক্তের চিহ্নমাত্র নেই তার ধমনিতে। প্রায় বছরখানেক পরে বার্লিনে এক ভোজসভায় তদানীন্তন জার্মান নাৎসি শিক্ষামন্ত্রী হিলবার্টকে কথাপ্রসঙ্গে হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, প্রফেসর, এ-কথা কি সত্য যে, ইহুদি বিতাড়নে আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গহানি হয়েছে?
হিলবার্ট তৎক্ষণাৎ জবাবে বলেছিলেন : আজ্ঞে না, অঙ্গহানি তো কিছু হয়নি!
উৎফুল্ল হয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, তাই বলুন! অথচ লোকে কত কথাই রটাচ্ছে!
হিলবার্ট বললেন, ওসব মূর্খলোকের কথায় কান দেবেন না, হের মিনিস্টার! অতীতের সেই গোটিনজেন আজ আর জীবিত নেই। মৃতদেহের আবার অঙ্গহানি কী?
মুখচোখ লাল হয়ে ওঠে শিক্ষামন্ত্রীর। জোর দিয়ে বলেন, ওই সাতজন ইহুদি অধ্যাপকের বদলে আমরা যদি সাতজন পাওয়ারফুল নর্ডিক প্রফেসরকে বহাল করি?
হিলবার্ট হেসে বলেন, হের মিনিস্টার! আপনাদের ওই পাওয়ার-পলিটিক্সটা আমি বুঝি না। আমি নেহাৎই অঙ্কের মাস্টার। আমি তো বুঝি : জিরো-টু-দি পাওয়ার সেভেন ইজুকালটু জিরো!
শিক্ষামন্ত্রী জবাব খুঁজে পাননি এ অঙ্কের!
***
জার্মানি থেকে এই ইহুদি-বিতাড়ন পর্বে একটি বিচিত্র ভূমিকা নিয়েছিলেন ওই হ্যান্স অ্যান্ডারসনের রূপকথার মানুষটি। প্রফেসর বোহর। গোটিনজেন-বার্লিনের পদচ্যুত ইহুদি অধ্যাপকেরা একের-পর-এক পত্র পেতে থাকেন তাঁর কাছ থেকে। অযাচিত নিয়োগপত্র। কোপেনহেগেন ল্যাবরেটরি থেকে। উপযুক্ত পদ খালি না থাকলে লিখতেন-সোজা এখানে চলে এসে ল্যাবরেটরিতে ঢুকে পড়ুন। আমার এখনও দু-বেলা দুমুঠো জুটছে, আপনারও জুটবে। আর কিছু না পান একটা তৈরি ল্যাবরেটরি তো পাবেন?
আশ্চর্য মানুষ! অধিকাংশই চলে গেলেন ডেনমার্কে। সেই যে-দেশের সমুদ্র উপকূলে বসে জলকন্যারা গান গেয়ে পালছেঁড়া হালভাঙা নাবিকদের হাতছানি দেয়। কেউ কেউ অতলান্তিকের ওপারে পাড়ি জমালেন। আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলি কুড়িয়ে নিল ক্ষ্যাপার ছুঁড়ে ফেলা পরশমণিগুলি। আইনস্টাইন যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী চাকরি নিয়ে চলে গেলেন তখন ফরাসি বৈং নিক পল স্যাঞ্জেভি লিখেছিলেন : ভ্যাটিকান ছেড়ে পোপ যদি আজ আমেরিকায় গিয়ে বসবাস শুরু করেন তাহলে খ্রিস্টান-জগতের যা অবস্থা হত, এই ঘটনার ইউরোপে বিজ্ঞান-জগতের ক্ষতি হল ততখানি।
মজার কথা—বিতাড়িত ইহুদি বিজ্ঞানীদের কেউই কিন্তু রাশিয়ায় গেলে না। বরং রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক গ্যামো, রোবিনোভিচ, ক্রিস্টিয়াকৌস্কির দল পাড়ি জমালেন আমেরিকায়। রাশিয়ায় স্তালিন ততদিনে লৌহ যবনিকা টেনে দিয়েছেন। তার ভিতরের খবর কেউ জানে না। একমাত্র কাপিৎজা আটকে পড়লেন সেখানে তিনি রাশিয়ায় গিয়েছিলেন কিছুদিনের জন্য। তাঁকে ফিরে আসতে দেওয়া হল না। কিন্তু আর দু-চারজন–যেমন হোটেম্যান–অর্থাৎ যাঁরা রাশিয়ায় পালিয়ে গিয়েছিলেন তাদের মরণাস্তিক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল রাশিয়ান পুলিসের হাতে। ধরে নেওয়া হয়েছিল তারা গুপ্তচর।
পৃথিবীর ইতিহাস ইতিমধ্যে অতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। মুসোলিনির ইটালির আগ্রাসী নীতিতে নাভিশ্বাস উঠেছে আবিসিনিয়ার, তোজোর জাপান ওদিকে টুটি টিপে ধরেছে পাশের বাড়ির–চিনের। এদিকে হিটলার একের পর এক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মাথায় পদাঘাত করে চলেছে। নাৎসি জার্মানির আগ্রাসী নীতির কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছে তারা। ব্রিটেন দিশেহারা, ফ্রান্স স্তম্ভিত, আমেরিকা নির্বিকার। একমাত্র স্তালিনের রাজ্যে কী হচ্ছে কেউ খবর পায় না।
কিন্তু না। রাজনীতি নয়, আমাদের লক্ষ্য অ্যাটম-বোমার বিবর্তন। সেদিকটায় নজর ফেরাই–
.
০৩.
1932 সালে রাদারফোর্ডের শিষ্য জেমস্ চ্যাডউইক আবার একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার করে বসলেন। সেজন্য নোবেল প্রাইজ দেওয়া হল তাকে।
নবাবিষ্কৃত বস্তুটির নাম : নিউট্রন!
নিউট্রন আবার কী? কোথায় পাওয়া যায়? না, নিউট্রন কোনো ধাতু-টাতু নয়-পরমাণুর কেন্দ্রস্থলের একটা অনাবিষ্কৃত অংশ। এই আবিষ্কারের ফলে পরমাণুর চেহারাটাই গেল পালটে–মানে বিজ্ঞানীদের ধারণায়। আগেই বলেছি, ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পরমাণুকে মনে করা হতো নিটোল, নিরেট,অবিভাজ্য কিছু একটা। প্রথম গোল বাধালেন রাদারফোর্ড-বলে বসলেন, না হে, পরমাণুতে অন্তত দুটি অংশ আছে। কেন্দ্রস্থলে ধনাত্মক বিদ্যুৎগর্ভ প্রোটন, আর তার বাইরে পাক-খেয়ে চলা ঋণাত্মক বিদ্যুৎগর্ভ ইলেকট্রন। তবে হ্যাঁ, নিরেট না হলেও পরমাণু অবিভাজ্য–ইলেকট্রন আর প্রোটন মিলে-মিশে এমনভাবে আছে যাতে তাদের আলাদা করা যাবে না। এবার ওই তালিকায় যুক্ত হল আর একটি নতুন শরিক–নিউট্রন। তাতে পরমাণুর খানদানি বদনখানি কেমন দাঁড়ালো?
এতদিনে সেটা পরিষ্কার হয়েছে। আমরা তা আগেই আলোচনা করেছি। অনেকটা সৌরজগতের মতো। পরমাণুর আকৃতি সম্বন্ধে নিখুঁত ধারণা দিলেন দিনেমার পণ্ডিত নীলস বোহর। তিনি বললেন, সৌরজগতের সঙ্গে পরমাণুর তুলনা করার সময় আরও একটা প্রভেদের কথা মনে রাখা উচিত। সৌরজগতের এক-এক কক্ষপথে একটিমাত্র গ্রহ থাকে; কিন্তু পরমাণুর ক্ষেত্রে এক-এক কক্ষ পথে একাধিক ইলেকট্রন সম-দূরত্ব বজায় রেখে পাক খায়। কেন্দ্র থেকে দূরত্ব অনুসারে নীলস বোহর কক্ষপথগুলিকে প্রথম কক্ষপথ, দ্বিতীয় কক্ষপথ ইত্যাদি নামকরণ করলেন। হিসাব করে দেখালেন–প্রথম কক্ষপথে দুটির বেশি ইলেকট্রন থাকতে পারে না, দ্বিতীয় কক্ষপথে থাকতে পারে না আটটির বেশি ইলেকট্রন, অনুরূপভাবে তৃতীয় কক্ষপথেও নোটিস জারি আছে : আঠারোজন ইলেকট্রন বসিবেক! এবং এ নোটিস রেল-কোম্পানির নোটিসের মতো ‘ব্যতিক্রমই আইনের পরিচায়ক’ নয়!
***
‘পিরিয়ডিক টেবল’ ধরে আমরা যদি হাইড্রোজেন থেকে পর পর মৌল পদার্থগুলির পরমাণুর আকৃতি লক্ষ্য করি, তাহলে দেখব কীভাবে এক-একটি কক্ষপথ পূর্ণ হয়ে যাবার পর নূতন কক্ষপথ আমদানি করতে হচ্ছে। হিলিয়ামে প্রথম কক্ষপথে ‘নো-ভেকেন্সি’ ঘোষিত হবার পরেই লিথিয়ামে যুক্ত হল দ্বিতীয় কক্ষপথ। তেমনি নিয়মে যেই দ্বিতীয় কক্ষপথ হাঁকল ‘ঠাই নাই ঠাই নাই ছোট সে তরী’ অমনি সোডিয়ামে আমদানি করতে হল তৃতীয় কক্ষপথ। (চিত্র 3)
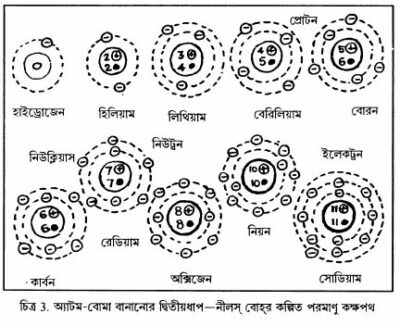
[চিত্র 3. অ্যাটম-বোমা বানানোর দ্বিতীয়পধাপ—নীলস বহর কল্পিত পরমাণু কক্ষপথ]
প্রফেসর বোহর আরও বললেন, যেখানে যেখানে কক্ষপথ পূর্ণ হচ্ছে সেই সেই মৌল পদার্থ স্থিতিশীল। সহজে রাসায়নিক মিশ্রণে তারা অংশ নিতে চায় না–ঠিক যেমন চাকরিতে যারা সদ্য পার্মানেন্ট হয়েছে, তারা শ্রমিক আন্দোলনে সামিল হতে চায় না। যেমন, হিলিয়াম, নিয়ন, আরগন, ক্রিপটন, জেনন প্রভৃতি; যাকে বলি–ইনার্ট।
বিজ্ঞানীরা আরও বললেন–ওই কেন্দ্র-অংশটা গোটা পরমাণুর তুলনায় আকারে খুবই ছোটো, অথচ গোটা পরমাণুর ওজনের বা ভরের প্রায় সবটাই আছে ওই কেন্দ্রে; কারণ ইলেকট্রনগুলির ভর খুব কম, তাতে শুধু বিদ্যুৎশক্তিই আছে। ওঁরা হিসাব করে প্রতিটি অংশের মাপ আর ওজন খাতা-কলমে বার করে ফেললেন। বললেন, গোটা পরমাণুর ব্যাসের দশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র হচ্ছে ওই কেন্দ্রের ব্যাস। আবার পরমাণু নিজেই এত ছোটো তা বোঝাতে বললেন, দৃশ্যমান আলোক-তরঙ্গ পরমাণুর তুলনায় হাজার গুণ বড়। এ-থেকে আপনার-আমার মতো সাধারণ মানুষের ধারণা হওয়া শক্ত! আসুন, একটা তুলনামূলক বিচার করি। মনে করুন ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ফাইনাল খেলা। দেখতে গিয়ে আপনি একঠোঙা মটর ভাজা কিনলেন। এখন ওই ফুটবলের মাঠটা যদি হয় গোটা পরমাণুর ক্ষেত্রফল তাহলে আধখানা মটরদানা হচ্ছে পরমাণুর কেন্দ্র বা নিউক্লিয়াসের ক্ষেত্রফল। সে হিসাবে দৃশ্যমান আলোকতরঙ্গ বেশ কয়েক কিলোমিটার লম্বা।
***
মোটকথা জেমস্ চ্যাডউইকের এই নবাবিষ্কৃত নিউট্রনই হচ্ছে আমাদের শেষ লক্ষ্যস্থল ওই পরমাণু-বোমায় পৌঁছানোর দু-নম্বর ধাপ।
কেন?–সেটা বোঝা যাবে ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক এনরিকো ফের্মির পরীক্ষার কথা যখন আমরা আলোচনা করব। আপাতত ফের্মি নয়, আমরা আলোচনা করি। নবযুগের নবীন কুরি-দম্পতির কথা। মাদাম কুরির কন্যা আইরিন কুরিও (1896 – 1956) মায়ের মতো রসায়ন-শাস্ত্রে পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। তিনি বিবাহ করেছিলেন ফ্রেডারিক জোলিও-কে (1900-1958)। ওঁরা স্বামী-স্ত্রী মিলে পরীক্ষা করছিলেন। ‘বোরন’ নিয়ে। বোরন একটি মৌল পদার্থ–ওঁরা অবশ্য পরীক্ষা করছিলেন বোরনের একটি আইসোটোপ নিয়ে, যার পারমাণবিক ওজন হচ্ছে দশ। তাতে আছে পাঁচটা প্রোটন ও পাঁচটা নিউট্রন। এই বোরনের ওপর হিলিয়াম আয়নের আঘাত হেনে ওঁরা পেলেন নাইট্রোজেনের এক জ্ঞাতিভাইকে, অর্থাৎ আইসোটোপকে–যার পারমাণবিক ওজন হচ্ছে তেরো। সাতটা প্রোটন ও ছয়টা নিউট্রন। ব্যাপার কী? হিসাবের কড়ি তত বাঘে খায় না! বোরনের ছিল দশ-কড়ি, তার সঙ্গে যোগ হল হিলিয়াম আয়নের চার কড়ি–হল গিয়ে একুনে চৌদ্দ-কড়ি। কেমন তো? কিন্তু পরীক্ষা শেষে ওঁরা পেলেন নাইট্রোজেন- আইসোটোপের তেরো-কড়ি। বাকি এককড়ি গেল কোথায়? কুরি-দম্পতি অনেক ভেবে বললেন, এই ফাঁকে বোরন-পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে একটা গামারশ্মি মুক্ত হয়েছে। সেটাই আমাদের নিরুদ্দিষ্ট ‘এককড়ি’! ওঁদের সূত্রটা হল :
B^10 + He^4 → N^13 + n^1
বোরন (10) + হিঃ আয়ন (4) নাইট্রোজেন (13) + সদ্যমুক্ত নিউট্রন (1)
ওঁরা আরও বললেন, তেরো বছর আগে লর্ড রাদারফোর্ড এই সূত্রেই পেয়েছিলেন নাইট্রোজেন থেকে অক্সিজেন। তিনিই প্রথম একটি ‘নিউট্রন’-কে বন্ধনমুক্ত করেছিলেন। তার চিত্রকল্পটা এইরকম—চিত্র 4 (জটিলতা এড়াতে নিউট্রনকে ছবিতে দেখানো হয়নি) :
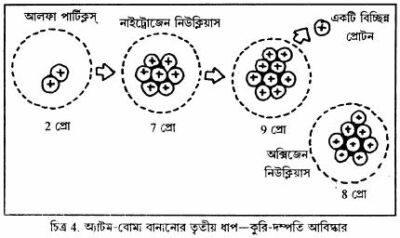
[চিত্র 4. অ্যাটম-বোমা বানানোর তৃতীয় ধাপ – কুরি-দম্পতি আবিষ্কার]
নিঃসন্দেহে কুরি-দম্পতির এই আবিষ্কার হচ্ছে পরমাণু-বোমা নির্মাণের পথে তিন নম্বর ধাপ। এবারেও কিন্তু ওই প্রচণ্ড সম্ভাবনার কথাটা কারও খেয়াল হয়নি। তিন বছর পরে (1935) ফ্রেডারিক জোলিও-কুরি সস্ত্রীক স্টকহমে গেলেন নোবেল পুরস্কার নিতে। অন্য একটি আবিষ্কারের জন্য–কৃত্রিম রেডিও-অ্যাকটিভিটির জন্য। সেখানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেছিলেন, “পদার্থের মৌলিক পরিবর্তন আজ প্রত্যক্ষ সত্য। এ থেকে প্রভূত শক্তির জন্ম হতে পারে।..এ কথা অনুমান করার যথেষ্ট যুক্তি আছে যে, বিজ্ঞানীরা যদি এভাবে মৌল পদার্থের পরমাণুকে ক্রমান্বয়ে বিচূর্ণ করতে পারেন তবে সদ্যমুক্ত শক্তি প্রচণ্ড শক্তিধর বিস্ফোরণের রূপ নিতে পারে…।”
কী আশ্চর্যের কথা! এতবড় ভবিষ্যৎবাণীতেও কিন্তু কোনো সাড়া জাগল না। তার প্রধান কারণ, যুক্তিটাকে আদৌ বিশ্বাসযোগ্য মনে করেনি কেউ। নোবেল-পুরস্কারপ্রাপ্ত জার্মান পণ্ডিত ওয়াল্টার নেস্ট এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, “মনে হচ্ছে দুনিয়াটা বুঝি একটা বারুদের স্কুপের ওপর বসানো! ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, দেশলাই কাঠিটার সন্ধান কেউ জানে না।”
রাদারফোর্ড তো জীবনের শেষদিন (1937) পর্যন্ত এই বিশ্বাস নিয়েই গেছেন যে, পরমাণু ভিতরকার ঘুমন্ত দৈত্যকে মানুষ কোনোদিনই জাগাতে পারবে না।
***
শুধু একজন বৈজ্ঞানিকের মনে কেমন যেন একটা খটকা লাগল। তার নাম লিও ৎজিলাৰ্ড, হাঙ্গেরিয় বৈজ্ঞানিক। পাঠকের স্মরণ থাকতে পারে, ইতিপূর্বে যে বারোজন বৈজ্ঞানিককে সন্দেহের তালিকায় রাখা হয়েছে পদার্থবিজ্ঞানী লিও ৎজিলাৰ্ড তার অন্যতম।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন বাধে (1914) তখন ৎজিলার্ডের বয়স মাত্র ষোলো বছর। বুদাপেস্টে টেকনিকাল অ্যাকাডেমির ছাত্র তখন তিনি। সামরিক আইনে বাধ্যতামূলক সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করতে হল ৎজিলাৰ্ডকে। কৈশোরে এবং যৌবনের প্রথম সামরিক কর্তাদের কাছ থেকে তিনি এমন সদ্ব্যবহার পেয়েছিলেন যে, সারাটা জীবনে তা ভোলেননি। অতি পরিণত বয়সে ৎজিলাৰ্ডকে একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, আপনি কী পেলে সবচেয়ে খুশি হন?
জবাবে ৎজিলাৰ্ড বলেছিলেন, ব্রাস-হেলমেট-মাথায় লাঠি মারার সুযোগ!
ৎজিলাৰ্ড আজন্ম সমর-বিরোধী।
প্রথম যুদ্ধ শেষে (1981) ৎজিলাৰ্ড এসেছিলেন জার্মানিতে। বাবা ছিলেন এঞ্জিনিয়ার, উনিও কৈশোরে বাস্তুবিদ হবার স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু বুদাপেস্ট থেকে বার্লিনে এসে ওঁর মত বদলে গেলো। উনি নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট হবার জন্য সচেষ্ট হলেন। তার কারণ বোধকরি কয়েকজন বিশ্ববিশ্রুত অধ্যাপকের প্রভাব। তিনি অধ্যাপক হিসাবে পেয়েছিলেন–আইনস্টাইন, নেস্ট, ফন-লে এবং প্ল্যাঙ্ককে; চারজনই নোবেল-প্রাইজ পাওয়া। হিটলার যখন জার্মানির ক্ষমতা দখল করল ৎজিলাৰ্ড তখন কাইজার উইলহেম ইন্সটিট্যুটের অবৈতনিক লেকচারার। তীক্ষ্ণধী ৎজিলাৰ্ড বুঝলেন, জার্মানির ভাগ্যাকাশে কালবৈশাখী প্রত্যাসন্ন। উনি চলে এলেন ভিয়েনায়। কিন্তু মাত্র দেড়মাসের মধ্যেই তার মনে হল অস্ট্রিয়াও যথেষ্ট নিরাপদ নয়–হিটলারের হাত থেকে অস্ট্রিয়ারও নিস্তার নেই। উনি পাড়ি জমালেন গ্রেট ব্রিটেনে। সেখানে থেকে পরে মার্কিন মুলুকে। মানহাটান প্রজেক্টের অন্যতম কর্ণধার হয়েছিলেন তিনি।
1933-সালে এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে লর্ড রাদারফোর্ড বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বললেন, ‘পরমাণুর ভিতরে সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করে মানুষের কাজে লাগাবার কথা যারা বলছে তারা বাতুল। সেদিন শ্রোতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পঁয়ত্রিশ বছরের লিও ৎজিলাৰ্ড। অনেক পরে স্মৃতিচারণে তিনি লিখেছেন, “সেই দিনই আমার মনে হল, লর্ড রাদারফোর্ড-এর কথা হয়তো ঠিক নয়। গত বছর জোলিও-কুরি বোরন থেকে একটি নিউট্রনকে মুক্ত করেছেন–এটা প্রত্যক্ষ সত্য। এর পর যদি কোনো বৈজ্ঞানিক এমন ব্যবস্থা করতে পারেন যাতে ক্রমান্বয়ে একের-পর-এক ওইভাবে নিউট্রন মুক্তি পাবে–তাহলে সেটা একটা চেন রি-অ্যাকশন’-এর রূপ নেবে। সেক্ষেত্রে পুঞ্জীভূত শক্তির পরিমাণটা বড় কম হবে না। প্রথমেই আমার মনে হয়েছিল ‘বেরিলিয়ামের কথা। পরে অন্যান্য মৌলিক পদার্থের কথাও মনে আসে, এমনকি ইউরেনিয়াম পর্যন্ত। কিন্তু বাস্তবে সে-সব পরীক্ষা করার সুযোগ আমি পাইনি-নানান কারণে ঘটে ওঠেনি।”
ৎজিলাৰ্ড সে পরীক্ষা সেদিন করেননি বটে তবে তিনিই বোধকরি প্রথম বৈজ্ঞানিক যিনি পরমাণুশক্তির সম্ভাবনাময় মনুষ্য-সভ্যতার অপরিসীম বিপদের কথা চিন্তা করেছিলেন এবং সেই আদিযুগেই তার প্রতিকারের কথা ভাবতে শুরু করেছিলেন। 1935-এ তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানীকে বলেছিলেন, অতঃপর পরমাণু বিভাজনের ব্যাপারটা গোপন রাখা উচিত।
বিস্মিত বৈজ্ঞানিকরা প্রতিপ্রশ্ন করেন : বল কী হে? বিজ্ঞানের আবিষ্কার আবার গোপন রাখা হবে কেন? কস্মিনকালেও তো এমনটা কেউ ভাবেনি?
-বুঝতে পারছেন না? পরমাণু শক্তিকে জনহিতকর কাজে লাগাবার আগেই যুদ্ধবিশারদের দল তা দিয়ে মারণাস্ত্র বানাতে চাইবে। জার্মান বৈজ্ঞানিকেরাই এ-বিষয়ে সবচেয়ে এগিয়ে আছেন। হিটলার যদি একবার এই শক্তির সন্ধান পায় তাহলে সে পৃথিবীটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে!
বৈজ্ঞানিকেরা বললেন, কী পাগলের কথা!
কেউ পাত্তা দিলেন না ৎজিলাৰ্ডকে।
বস্তুত সেটা এমন একটা যুগ যখন বৈজ্ঞানিকেরা রাজনীতির ধার ধারতেন না। ল্যাবরেটরির বাইরে যে একটা জগৎ আছে এটা মনেই থাকত না তাদের। অপরপক্ষে রাজনীতিবিদেরাও বৈজ্ঞানিকদের বড় একটা পাত্তা দিতেন না। সাধারণ মানুষ রাজনীতি নিয়ে যতটা মাতামাতি করত বিজ্ঞান নিয়ে তার শতাংশের একাংশও করত না। দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আলোচনার আসরে হিটলারের নাম যদি লক্ষ বার উচ্চারিত হয় তবে ‘নিউট্রন’ শব্দটা উচ্চারিত হয় একবার!
আমরা ইতিমধ্যে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে 1932-33 সাল পর্যন্ত এগিয়ে এসেছি। এসে পৌঁচেছি এমন একটি খণ্ডমুহূর্তে যখন বিশ্বের তিন প্রান্তে তিনটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটছে। এক নম্বর–কেমব্রিজের ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবরেটরিতে চ্যাডউইকের সূতিকাগারে জন্ম নিল ‘নিউট্রন’ (ফেব্রুয়ারি 1932); দু নম্বর-রুজভেল্ট আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলেন (নভেম্বর 1932), এবং তিন নম্বর–হিটলার জার্মানির সর্বময় কর্তা হল (জানুয়ারি 1933)।
.
০৪.
ইংলন্ডে যেমন রাদারফোর্ড, ডেনমার্কে যেমন নীলস বোহর, ফ্রান্সে যেমন কুরি-দম্পতি তেমনি ইটালির সবচেয়ে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন এনরিকো ফের্মি। তার অনুগামীরা তাকে বলত, ‘পোপ অব ফিজিক্স’। বৈজ্ঞানিক সমারফেল্ড-এর (1868-1951) শ্রেষ্ঠ ছাত্র পরবর্তী যুগের নোবেল-লরিয়েট জার্মান ফিজিসিস্ট হান্স বেথে (1906 ) রোম থেকে তার গুরুকে চিঠিতে এই সময়ে লিখেছিলেন, “রোমে এসে কলিসিরাম তো দেখলামই কিন্তু সবচেয়ে অবাক হয়েছি এনরিকো ফের্মিকে দেখে। তাকে যে কোনো প্রশ্নই দেওয়া যাক অবধারিতভাবে তার সমাধানটা তার নজরে পড়ে। অদ্ভুত প্রতিভা!” জোলিও-কুরি আলফা-পার্টিক-এর আঘাতে পরমাণুর প্রাথমিক নিদ্রা ভাঙিয়েছেন শুনে ফের্মি সিদ্ধান্ত নিলেন চ্যাডউইকের নব-আবিষ্কৃত ওই নিউট্রন দিয়ে আঘাত করে তার নিদ্রাটা ভাঙা যায় কিনা দেখবেন। স্থির করলেন, একের-পর-এক মৌল পদার্থ নিয়ে তিনি পর পর পরীক্ষাকার্য চালিয়ে যাবেন!
যে-কথা সেই কাজ। প্রথম আটটি পরীক্ষায় কোনো ফল পাওয়া গেল না; কিন্তু নবম মৌল পদার্থ ফুরিনের ক্ষেত্রে গাইগার-কাউন্টার যন্ত্রে কাটাটা দুলতে শুরু করল। এ যন্ত্রটি হ্যান্স গাইগার (1882-1945) আবিষ্কার করেছিলেন কয়েক বছর আগে (1908-10)–এতে অদৃশ্য রেডিও-অ্যাকটিভিটি ধরা পড়ে। অর্থাৎ ফের্মির পরীক্ষায় দেখা গেল, নিউট্রন দিয়ে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করলেও কৃত্রিম রেডিও-অ্যাকটিভিটি জন্মাতে পারে-যার মানে হল, পরমাণুটি বিচূর্ণ হয়ে গেছে। এবং অন্যান্য মৌল-পদার্থের আইসোটোপ জন্ম নিচ্ছে! ফের্মি আরও অনেকগুলি মৌল পদার্থ নিয়ে পরীক্ষা করলেন–এমনকি সবচেয়ে ভারী পদার্থ ইউরেনিয়াম নিয়েও। ওঁর ধারণা হল–ইউরেনিয়াম ওঁর বীক্ষণাগারে নূতন ধাতুর জন্ম দিল–যা নাকি তদানীন্তন বিজ্ঞানজগতের জ্ঞাত বিরানব্বইটি ধাতুর মধ্যে নেই–অর্থাৎ তার দাবি : নূতন ধাতুর জন্ম দিয়েছেন তিনি–যাকে বলে transuranic element, ইউরেনিয়ামোত্তর ধাতু।
ফের্মির দাবি শেষ পর্যন্ত টেকেনি। নূতন ধাতুর জন্ম তিনি দিতে পারেননি। তা বলে ফের্মির এ পরীক্ষা অকিঞ্চিৎকর নয়। বস্তুত তিনি এ পরীক্ষায়–এবং তিনিই সর্বপ্রথম ইউরেনিয়াম পরমাণুকে বিচূর্ণ করলেন। চ্যাডউইক-আবিষ্কৃত নিউট্রনের কার্যকারিতা তিনি প্রমাণ করলেন। সেদিন কেউ টের না পেলেও এ কাজটি পরমাণু-বোমা নির্মাণের চতুর্থ সোপান।
***
অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই সেদিন ভেবেছিলেন ফের্মি ইউরেনিয়ামোত্তর কোনো ধাতুকে জন্ম দিয়েছেন। দিকে দিকে দেশে দেশে সবাই ফের্মির প্রশংসায় পঞ্চমুখ। একমাত্র একজন এ দাবিতে সন্দেহ প্রকাশ করে বসলেন–জার্মান-দম্পতি ইডা (1896-1978) আর ওয়ালটার (1893-1960) নোডাক। ফ্রাউ ইডা নোডাক একজন অদ্ভুত রসায়নবিদ মহিলা। 1925-এ তাঁরা ‘রেনিয়ান’ নামে একটি ধাতু যখন আবিষ্কার করেছিলেন। এই 30-32 বয়সের স্বামী-স্ত্রী একই বছরে (1925) আবিষ্কার করেন আরো একটি ধাতু-মাসুরিয়াম (আর নাম হয়ে টেকনেটিয়াম)। সেই ইডা নোকই সাহস করে বললেন–ফের্মি কোনো ইউরেনিয়ামোত্তর ধাতুর সন্ধান বোধ হয় পাননি, অপরপক্ষে হয়তো তিনি পরমাণুর কেন্দ্রস্থলটি অর্থাৎ নিউক্লিয়াসটিকে দু টুকরো করে ফেলেছেন, নবাবিষ্কৃত ইউরেনিয়ামোত্তর ধাতু যেটাকে বলা হচ্ছে, আসলে সেটা কোনো পরিচিত মৌল পদার্থের আইসোটোপ।
শ্ৰীমতী নোডাক ঠিকই বলেছিলেন; কিন্তু কোনো বৈজ্ঞানিক তখন সেটা মেনে নিতে পারেননি। ফের্মি নিজে তো নয়ই, এমন কি জার্মানির অটো হান (1879 – 1968) অথবা ইংল্যান্ডের রাদারফোর্ডও নয়। শ্রীমতী নোক দুঃখ করে লিখেছিলেন, “আমি এবং আমার স্বামী প্রফেসর হানকে একথা যখন বোঝাতে চাইলাম তখন তিনি তাতে কানই দিলেন না। আমরা বলতে চেয়েছিলাম, বৈজ্ঞানিক ফের্মির ওই নিউট্রন আসলে পরমাণুর কেন্দ্রবিন্দুকে বিদীর্ণ করেছে। কেউই সেদিন সেটা মেনে নেননি।”
দুঃখের কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু এজন্য দোষও দেওয়া যায় না অটো হান অথবা অন্যান্য বৈজ্ঞানিকদের। তার কারণটা বুঝিয়ে বলি। এতদিন লক্ষ লক্ষ ইলেকট্রনভোল্ট শক্তিবহ আলফা পার্টিকল্স-এ অথবা প্রোটন দিয়ে পরমাণুর কেন্দ্রস্থলটি বিদীর্ণ করার চেষ্টায় কেউ সফলকাম হতে পারেননি। সেক্ষেত্রে কে বিশ্বাস করবে নিউট্রন–যার শক্তি এক ইলেকট্রন-ভোল্টেরও কম–তা ওই পরমাণুর কেন্দ্রকে বিচূর্ণ করেছে? ধরুন একটি সৈন্যদল দীর্ঘদিন কামান বর্ষণে একটা দুর্গপ্রাকার বিধ্বস্ত করতে পারল না, তারপর একজন এসে বললে-”স্যার, কামানের গোলার বদলে এবার পিংপঙের বল ছুঁড়ে দেখলে হয় না?” তাহলে সেনাপতি কী বলতে পারেন?
বস্তুত কামানের গোলা যা পারেনি, পিংপঙের বল সেটাই করেছিল ফের্মির গবেষণাগারে। এবার রঙ্গমঞ্চে এসে অবতীর্ণ হলেন শ্রীমতী নোডাক-এর বদলে আর দুজন প্রতিদ্বন্দিনী।
***
মাদাম কুরির কন্যা ফরাসি বৈজ্ঞানিক আইরিন কুরি ব্রাসেলস্ সম্মেলনে ওই একই কথা বললেন। প্রফেসর অটো হান, বিশেষ করে তার সহকর্মী এবং শিষ্যা কুমারী মাইট্রার (1878-1968) দৃঢ়স্বরে বললেন, নিউট্রনের পক্ষে পরামাণুর কেন্দ্র বিদীর্ণ করা আদৌ সম্ভবপর নয়। ফ্রয়লাইন মাইটনার সম্মেলনকে জানালেন, তিনি বারে বারে পরীক্ষাটা করে দেখছেন। শ্রীমতী কুরির দাবি মেনে নেওয়া চলে না।
শ্ৰীমতী আইরিন কুরি তার স্মৃতিচারণে বলেছেন, একমাত্র নীলস বোহর ছাড়া কেউ সেদিন আমাদের স্বামী-স্ত্রীর কথায় আদৌ পাত্তা দেননি।
সম্মেলনে থেকে ফিরে এসে শ্রীমতী কুরি আবার ওই পরীক্ষাগুলি করে দেখলেন তার পারি-ল্যাবরেটারিতে। আবার ওই একই ফল পেলেন। এবার তিনি পরীক্ষার বিবরণ ছাপিয়ে দিলেন একটি বিখ্যাত বিজ্ঞানের পত্রিকায়।
অটো হান সেটা পড়ে নাকি বলেছিলেন, “শ্রীমতী আইরিন কুরি তাঁর মায়ের কাছ থেকে শেখা রসায়নবিদ্যার ওপর বেশি জোর দিতে চাইছেন। তার মা মাদাম-কুরি ছিলেন অসীম প্রতিভাশালী এক মহীয়সী বিজ্ঞানী, কন্যাও মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে রসায়নবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রসায়ন এ-কয়েক বছরে আরও অনেকটা এগিয়ে গেছে।“
প্রফেসর অটো হান তখন জার্মানির সবচেয়ে বড় রসায়ন-বিজ্ঞানী। তার এ কথায় নিশ্চয়ই মর্মাহত হয়েছিলেন শ্রীমতী কুরি–কিন্তু তিনি নীরবই রইলেন। পরে বোধ হয় প্রফেসর হান ভেবেছিলেন ওই ফরাসি বৈজ্ঞানিক-দম্পতিকে উপহাস্পদ করা ঠিক হবে না। তিনি একটি ব্যক্তিগত পত্র লিখলেন পারিতে। লিখলেন, “আমার মনে হয় আরও সাবধানতা নিয়ে তোমাদের এ পরীক্ষাগুলি করে দেখা উচিত। তারপর কাগজে প্রবন্ধ লেখবার প্রশ্ন উঠবে। তোমরা যা বলছ, তা যে অসম্ভব একথা তো তোমরা নিজেরাই বুঝছ। ইলেকট্রো-নিউট্রাল নিউট্রনের দ্বারা অসীম বিদ্যুদর্গৰ্ভ নিউক্লিয়াস কখনও বিদীর্ণ হতে পারে? আমার অনুরোধ–আরও গভীরভাবে পরীক্ষা করার পূর্বে তোমরা আর কোনো প্রবন্ধ প্রকাশ কর না।”
কুরি-দম্পতি প্রবীণ অধ্যাপকের ওই পত্রটির কোনো প্রত্যুত্তর করলেন না। অপরপক্ষে ঠিক পরবর্তী সংখ্যা বিজ্ঞান-পত্রিকায় পুনরায় ছাপা হল দ্বিতীয় একটি প্রবন্ধ!
রীতিমতো ক্ষেপে গেলেন অটো হান। হয়তো কিছু একটা করে বসতেন, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই তার জীবনে ঘটল একটা মর্মান্তিক ঘটনা। বিহ্বল হয়ে পড়লেন অটো হান। গোপনে তাঁর এক ছাত্র এসে তাকে জানিয়ে গেলো–হিটলারের গেস্টাপো-বাহিনী সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে প্রফেসর হান-এর একান্ত সহচরী এবং দক্ষিণ হস্তস্বরূপা মিস লিজা মাইটনার পুরোপুরি আর্য নন! যে কোনো মুহূর্তে তাকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে। অটো হানের সঙ্গে কুমারী মাইটনারের সম্পর্কটা ছিল নিবিড়। কতটা ঘনিষ্ঠ তো জানি না; কিন্তু ওঁর ডালহেম-ইন্স্যুটের যাবতীয় দায়িত্ব বহন করতেন ওই প্রিয়শিষ্যা। মাথায় হাত দিয়ে বসলেন অটো হান। উনি ছুটে গেলেন প্রফেসর ম্যাক্স প্লাঙ্কের কাছে। কোয়ান্টাম-থিয়োরির (1900) জনক ম্যাক্স প্লাঙ্ক-এর নাম কে না জানে? দুজনে পরামর্শ করে সরাসরি চলে এলেন বার্লিনে। দেখা করলেন খাস ফুরারের সঙ্গে–অ্যাডলফ হিটলারের সঙ্গে। বললেন, কুমারী মাইটনার-এর অভাবে জার্মানির সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান মন্দিরের বনিয়াদ ধসে যাবে। সেটা জার্মানিরই নিদারুণ ক্ষতি!
অ্যাডলফ হিটলার নাকি জবাবে বলেছিলেন, প্রফেসর, আপনাদের বিজ্ঞান জগতের সঠিক হিসাব আমি জানি না। আপনারা কি মনে করেন এই ফ্ৰয়লাইন লিজা মাইটনার-এর পাণ্ডিত্য সেই ইহুদি-বাচ্চা আইনস্টাইনের চেয়েও বেশি?
নতমস্তকে ফিরে এলেন হান আর প্লাঙ্ক, বার্লিন থেকে ডালহেম। সামনেই গ্রীষ্মবকাশের ছুটি। দলে দলে সবাই বেড়াতে যাচ্ছে। কুমারী মাইটনার সেই সুযোগে চলে গেলেন (1938) সুইডেনে, গ্রীষ্মবকাশ কাটাতে। ডালহেম ইন্সটিট্যুটের কেউ তাদের এই সর্বময়ী কত্রীর প্রস্থানে বিদায় জানাতে এল না–তারা জানত, উনি কয়েক সপ্তাহের জন্য গোটিনজেন-এ বেড়াতে যাচ্ছেন। প্লাঙ্ক, হান আর মাইটনার নিজে শুধু জানতেন–এই তাঁর চিরবিদায়! ল্যাবরেটারির যন্ত্রপাতি, ব্যক্তিগত স্মৃতিচিহ্ন, এমনকি অসমাপ্ত রিসার্চের কাগজপত্রগুলোও সঙ্গে নেওয়া গেল না। একটিমাত্র স্যুটকেস হাতে প্রফেসার হানের মানসকন্যা চিরকালের জন্য। গ্রীষ্মবকাশ কাটাতে চলে গেলেন!
শ্রীমতী মাইটনার নেই, তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন প্রফেসর হানের আর এক প্রিয়-শিষ্য–স্যাসম্যান। ডালহেম ইন্সটিটুটে তিনিই হলেন হানের দক্ষিণ-হস্ত। প্রফেসর হান ল্যাবরেটারির দ্বিতলে নিজ কামরাতেই দিন কাটান–একতলার ল্যাবরেটারিতে বড় একটা আসেন না। মনটা ভেঙে গেছে তার। সত্যই তো, জার্মানির পক্ষে আলবার্ট আইনস্টাইন যতটা অপরিহার্য ছিলেন কুমারী মাইটনার নিশ্চয় ততটা ছিলেন না কিন্তু গোটা জার্মানি নয়, এই ডালহেম ইন্সটিট্যুটে সেই বিজ্ঞানভিক্ষুণীর স্থান যে কতটা অপরিহার্য তা একমাত্র তিনিই জানতেন।
***
মাসখানেক পরের কথা। প্রফেসর হান কী একটা বই পড়ছিলেন তার খাসকামরায়; দ্বিতলের ঘরে। চুরুটের ধোঁয়ায় ঘরটা আগ্নেয়গিরির রূপ নিয়েছে। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন স্ট্র্যাসম্যান! বললেন প্রফেসর, এই প্রবন্ধটা পড়ে দেখুন!
স্ট্র্যাসম্যান তার স্মৃতিচারণে ঘটনাটি সম্বন্ধে লিখেছেন :
“আমার হাতে ছিল একটি বিজ্ঞান-বিষয়ক পত্রিকা। তাতে বার হয়েছে আইরিন-জোলিওর তৃতীয় প্রবন্ধ। ওঁরা তাদের পরীক্ষার ফলাফল পুনরায় প্রকাশ করে বলতে চেয়েছেন, ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসে নিউট্রন ‘বোম্বার্ড’ করে তারা পেয়েছেন ‘ল্যানথেনাম’ ধাতু। অর্থাৎ ইউরেনিয়াম পরমাণু পুনরায় বিদীর্ণ করেছেন তারা। আমি জানতাম, প্রফেসার হান থিয়োরিটা বিশ্বাস করেননি; জোলিও-দম্পতিকে এ বিষয়ে পত্রিকায় কিছু ছাপতে বারণও করেছিলেন তিনি। তবু এই তৃতীয় প্রবন্ধটা পড়ে আমার মনে হয়েছিল–ফরাসি-দম্পতিই ঠিক কথা বলছেন। তাই পত্রিকাটি হাতে নিয়ে আমি ছুটে চলে এসেছিলাম প্রফেসার হানের ঘরে। উনি কী একটা বই পড়ছিলেন। কেমন যেন ক্লান্ত, বিষণ্ণ। আমার উত্তেজনাতেও ওঁর কোনো ভাবান্তর হল না। বললেন, কী ওটা?
“আমি বাড়িয়ে ধরলাম পত্রিকাটা। বললাম, জোলিও-কুরি দম্পতির তৃতীয় প্রবন্ধ। ওঁরা পুনরায় নিউক্লিয়ার ফিশান করে প্রমাণ করেছেন।
“আমাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে প্রফেসর বললেন, আমার সময় নষ্ট কর না। ওই ফরাসি বান্ধবীটির প্রবন্ধ পড়ার মতো সময় এবং ধৈর্য আমার নেই!
“আমি কিন্তু নাছোড়বান্দা। বিনা অনুমতিতেই প্রবন্ধের মূলতত্ত্বটা জোরে জোরে পড়তে থাকি। জেদি বাচ্চা ছেলের মতো প্রফেসর হান তার ঘূর্ণমান চেয়ারে আধখানা পাক খেলেন। একশো আশি ডিগ্রি। উল্টো দিকে ফিরে চুরুট ফুঁকতে থাকেন। তা হোক, শুনতে তো পাচ্ছেন। আমি পড়েই চলি। হঠাৎ একশো আশি ডিগ্রিকে তিনশো ষাট ডিগ্রি করে বসলেন। ছিনিয়ে নিলেন পত্রিকাটি আমার হাত থেকে। চুরুটটা নামিয়ে রেখে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন প্রবন্ধটার ওপর। কয়েক মিনিট গোগ্রাসে গিলতে থাকেন প্রবন্ধটা। তারপর কোথাও কিছু নেই লাফ দিয়ে উঠে পড়লেন উনি। দুদ্দাড়িয়ে নেমে এলেন সিঁড়ি দিয়ে। ঢুকে পড়লেন ল্যাবরেটারিতে। আমি ওঁর পিছন পিছন। অর্ধসেবিত চুরুটটা যে পড়েই রইল ওঁর টেবিলে সে-কথা আমাদের খেয়াল ছিল না।
“এরপর পাক্কা তিন সপ্তাহ আমরা দুজনে ল্যাবরেটারি থেকে আদো বার হইনি। ল্যাবরেটারি-সংলগ্ন বাথরুম ছাড়া কোথাও যাইনি–এমন কি সংবাদপত্রও পড়িনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কফি-স্যান্ডউইচ খেয়েছি, বীক্ষণাগারে ডিভ্যানে পালা করে এক-আধটু ঘুমিয়ে নিয়েছি। কুরি-দম্পতির তিন মাস ধরে সম্পন্ন করা প্রতিটি পরীক্ষা অধ্যাপক হান তিন সপ্তাহে নিজে হাতে করে দেখলেন। তারপর একদিন আমার হাতখানা টেনে নিয়ে বললেন, স্ট্যাসম্যান, আমি স্বীকার করছি! অটো হান-এর ভুল হয়েছিল, আইরিন কুরির নয়!
“সে এক অবিস্মরণীয় মুহূর্ত! যেন একটা কামানের গোলা পরাজয় স্বীকার করছে পিংপং বলের কাছে!
“আমি একা এ ঘটনার সাক্ষী; কিন্তু একটি জ্বলন্ত প্রমাণ আমার হাতে আছে। আক্ষরিক অর্থে। প্রফেসর হানের খাসকামরায় সেই টেবিলক্লথে অর্ধদগ্ধ চুরুটটা তিল তিল করে প্রমাণ করেছে পিংপং বলের সঙ্গে দ্বৈরথ-সমরে কামানের গোলার পরাজয় কাহিনি! জ্বলন্ত প্রমাণ!”
***
একটা কথা। কুরি-দম্পতির একটা ভুল হয়েছিল। তারা বলেছিলেন, ইউরেনিয়াম বিদীর্ণ করে তারা পেয়েছেন ল্যানথেনাম। সেটা ভুল। তারা বাস্তবে পেয়েছিলেন ‘বেরিয়াম’। অথচ সেটা ধরতে পারেননি। পারলে, আরও নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হতেন তারা। প্রফেসর হানের পাকা হাতে এ ত্রুটি ধরা পড়ে গেলো। তাই তিনিই পেলেন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের সত্যটা। তাই বলা হয়–প্রফেসর অটো হানই সজ্ঞানে প্রথম ইউরেনিয়াম-পরমাণুকে বিদীর্ণ করলেন।
আমাদের অ্যাটম-বোমার বিবর্তনে এইটা হল পঞ্চম সোপান! মজা হচ্ছে এই যে, পরীক্ষার সাফল্যটাকে কিন্তু তখনকার বিজ্ঞানসূত্র অনুসারে যুক্তি দিয়ে মেনে নেওয়া যাচ্ছিল না। ইউরেনিয়াম ভেঙে উনি তার কাছাকাছি কোনো মৌল পদার্থ পেলেন না; পেলেন, ‘বেরিয়াম’–যার পারমাণবিক ভর’ বা অ্যাটমিক ওয়েট ইউরেনিয়ামের প্রায় অর্ধেক! এমনটা তো হওয়ার কথা নয়! পদার্থবিদ্যা এর কোনো ব্যাখ্যাই দিতে পারে না, অথচ রসায়ন-বিদ্যা বলছে ওটা বেরিয়াম ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। এ কী বিড়ম্বনা! তা হোক, তবু প্রফেসর হান তার পরীক্ষার ফলাফল তৎক্ষণাৎ ছাপতে দিলেন। তারিখটা বাইশে ডিসেম্বর 1938।
তার বিশবছর পরে প্রফেসর হান একজন সাংবাদিককে বলেছিলেন, প্রবন্ধটা ডাকে দেবার পর আমার এমনও মনে হয়েছিল পোস্ট-আপিসে গিয়ে ওটা ফেরত নিয়ে আসি। কারণ আমার পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফলটা আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।
প্রফেসর হান আরও একটি কাজ করলেন। তার প্রবন্ধের একটি কপি, ছাপা হওয়ার আগেই পাঠিয়ে দিলেন তার এতদিনের বান্ধবী কুমারী মাইটনারকে। লিজা মাইটনার তখন সুইডেনের দক্ষিণপ্রান্তে সমুদ্রতীরের একটি ছোট্ট জনপদে নির্বাসিতা। একা একাই ছিলেন এতদিন। মাত্র কয়েকদিন আগে তাকে সঙ্গ দিতে এসেছেন তার বোনপো ডক্টর অটো রবার্ট ফ্রি (1904-1979)। তিনিও প্রথম শ্রেণির পদার্থবিজ্ঞানী। জার্মানি থেকে বিতাড়িত হয়ে আশ্রয় পেয়েছিলেন কোপেনহেগেন-এ, প্রফেসর নীলস বোহর-এর ছত্রছায়ায়। ফ্রিশ এসেছিলেন নিতান্ত ছুটি কাটাতে–মাসিমাকে এ দুর্দিনে সঙ্গ দিতে। কিন্তু সেই শুভলগ্নেই একদিন মাসিমার নামে এসে পৌঁছলো একটা মোটা খাম–জার্মানি থেকে। সেটা পড়ে মাসিমা যেন খেপে উঠলেন। ফ্রিশকে বোঝাতে থাকেন সবকিছু। ফ্রিশ প্রথমটা কর্ণপাত করতে চাননি–কিন্তু মাসিমার নির্বাতিশয্যে শেষপর্যন্ত দুজনে মিলে প্রবন্ধটা পড়ে ফেললেন। প্রথমটা বিশ্বাসই হতে চায়নি ফ্রিশ-এর; কিন্তু ওঁর মাসিমা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ওঁকে বুঝিয়ে দিলেন ব্যাপারটা।
ছুটি কাটাতে এসে, অদ্ভুত এক সত্যকে আবিষ্কার করলেন ডক্টর ফ্রি। উনি এইসময় সুইডেন থেকে ওঁর মাকে চিঠি লিখেছিলেন, “সুইডেন-এর পাইন জঙ্গলে হাতি পাওয়া যায় বিশ্বাস কর? এখানে এসে দেখি তোমার দিদি জঙ্গলে একটা হাতি ধরে ফেলেছেন। আমরা দুজনে হাতিটার ল্যাজ চেপে ধরেছি–কিন্তু এতবড় জন্তুটাকে নিয়ে কী করব বুঝে উঠতে পারছি না!”
মাসখানেক পরে ডক্টর ফ্রিশ ফিরে এলেন ডেনমার্কে। প্রথমেই ছুটে চলে গেলেন প্রফেসর নীলস বোহর-এর কাছে। সবিস্তারে সব কথা খুলে বললেন। প্রফেসর অটো হানের পরীক্ষার ফলাফল এবং মিস মাইটনারের ব্যাখ্যা। ফলশ্রুতি হাতে হাতে! প্রফেসর বোহর নির্বাক শুনছিলেন এতক্ষণ। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই আচমকা এক ঘুষি মেরে বসলেন ছাত্রকে! টাল সামলে নিয়ে ডক্টর ফ্রি বুঝতে পারেন–এটা আনন্দের অভিব্যক্তি। প্রফেসর বোহর দু-হাত শূন্যে তুলে তখন। বলছেন : মূর্খ! মূর্খ আমরা! এত সোজা ব্যাপারটা এতদিন ধরতে পারিনি!
***
অটো হান অথবা নীলস বোহর-এর মতো নোবেল-লরিয়েট বৈজ্ঞানিক যে সমস্যার কিনারা করতে সেদিন দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন আজ কিন্তু আপনি-আমি সেটা সহজেই বুঝতে পারব–মোটামুটি ব্যাপারটা।
প্রথম সমস্যা ছিল সেই বিভ্রান্তিকর প্রশ্নটা–কামানের গোলা যা পারেনি তা পিংপঙের বল কেমন করে করল?
1919 সালে নাইট্রোজেন পরমাণুর অন্তর বিদীর্ণ করতে রাদারফোর্ড ব্যবহার করেছিলেন অত্যন্ত দ্রুতগামী আলফা পার্টিকলস্। পরে জন কক্ৰক্ট (1897 – 1967) চেষ্টা করেছিলেন প্রোটন দিয়ে। যেহেতু আলফা-পার্টিকলস এবং প্রোটন হচ্ছে বিদ্যুৎগর্ভ এবং নিউট্রন বিদ্যুৎবিচারে নিরপেক্ষ, তাতেই এই সংশয়টা জেগেছে। কিন্তু বস্তুত সংশয়ের কোনো অবকাশ এখানে নেই। পরমাণুর কেন্দ্রে আছে ধনাত্মক বিদ্যুৎ; অপরপক্ষে আলফা-পার্টিকলস্ এবং প্রোটন দুটিই হচ্ছে ধনাত্মক। তাতেই ওঁদের অসুবিধা হচ্ছিল। সহধর্মী বিদুৎকণা পরস্পরকে দূরে ঠেলে। তাই ধনাত্মক বিদ্যুৎগর্ভ আলফা-পার্টিকলস্ অথবা প্রোটনকে পরমাণুকেন্দ্র দূরে ঠেলে দিচ্ছিল। ব্যাপারটার চিত্ররূপ হচ্ছে চিত্র-5 এর মতো।
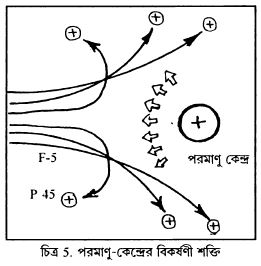
[চিত্র-5. পরমাণু-কেন্দ্রের বিকর্ষনী শক্তি]
এখানে আমরা পাশাপাশি ছয়টা আলফা-পার্টিকলস-এর গতিপথ দেখিয়েছি। পরমাণু কেন্দ্রের কাছাকাছি এসেই বিকর্ষণী-শক্তিতে সেগুলি বেঁকে গেছে। মাঝের দুটি বুলেট তো একেবারে প্রতিহত হয়ে উল্টোদিকে ফিরে গেছে। ফলে লক্ষ্যভেদ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কম। চ্যাডউইক কর্তৃক নবাবিষ্কৃত নিউট্রন যেহেতু বিদ্যুৎ-নিরপেক্ষ তাই তাকে এভাবে কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎশক্তি ঠেলে দেয়নি। তাই ফের্মির ল্যাবরেটারিতে নিউট্রন পরমাণুর কেন্দ্রটি বিদীর্ণ করতে পেরেছিল। কামানের গোলাকে হারিয়ে দিয়েছিল পিংপং-এর বল!
***
দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে, অটো হান ইউরেনিয়ামের পরমাণু বিদীর্ণ করে কেমন করে ‘বেরিয়াম’ পেলেন? এবার সেটাই বুঝবার চেষ্টা করব আমরা :
উনি পরীক্ষা করছিলেন ‘ইউরেনিয়াম-235’ নিয়ে, যাকে সংক্ষেপে বলে ইউ(U)-235। তার চেহারাটা কেমন? কেন্দ্রস্থলে আছে 92টি প্রোটন (-) এবং 143টি নিউট্রন (নিরপেক্ষ) আর বাইরে একাধিক কক্ষপথে সর্বমোট 92টি ইলেকট্রন (-)। এমন একটি পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে বাইরে থেকে এসে প্রচণ্ড আঘাত হানল একটি নিউট্রন। তাতে কেন্দ্রস্থলটি দু-টুকরো হয়ে গেলো।
জীববিজ্ঞানের বইতে ‘অ্যামিবা কেমন করে দু-টুকরো হয়, তার ছবি নিশ্চয়ই দেখেছেন। ব্যাপারটা হল অনেকটা ওই রকম। দুটি ভাগে যত প্রোটন থাকবে তার যোগফল হবে 92। দু-টুকরো হয়ে যাওয়া প্রতিটি কেন্দ্রের চারপাশে ইলেকট্রনগুলি নূতন করে ঘুরতে শুরু করবে–যে ভাগে যতগুলি প্রোটন আছে সেই ভাগে ততগুলি ইলেকট্রন যুক্ত হবে, যাতে ঋণাত্মক আর ধনাত্মক বিদ্যুতের পরিমাণ দুটি নবলব্ধ পরমাণুতে সমান হয়। ওই সঙ্গে আরও একটি কাণ্ড ঘটে—কেন্দ্রস্থলের গুটি তিন নিউট্রন বিচ্ছিন্ন হয়ে এদিক-ওদিক ছুটে যায়। আরও একটি কাণ্ড ঘটে-পরমাণু বিদীর্ণ হওয়ায় ক্ষণিকের জন্য প্রচণ্ড শক্তি উদ্ভূত হয়। এই ব্যাপারটাই চিত্র 6-এ বোঝানো হয়েছে। এখানেও চিত্রে নিউট্রন দেখানো হয়নি।
তাই যদি হবে, তবে ফের্মি অথবা অটো হানের ল্যাবরেটারিটা বিস্ফোরণে উড়ে গেল না কেন? আইনস্টাইনের সেই E = mc^2 ফর্মূলামতো তো শুনেছিলাম এক গ্রাম পরিমাণ বস্তুর বিনাশে চার-হাজার টন কয়লার দাহ্যশক্তির সমতুল শক্তির জন্ম হবে।
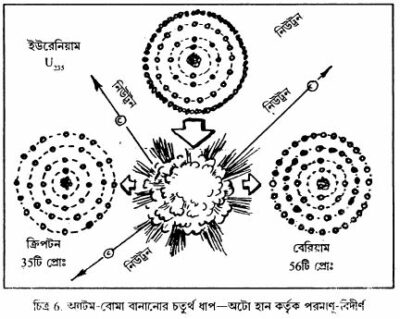
[চিত্র 6. অ্যাটম-বোমা বানানোর চতুর্থ ধাপ–-অটো হান কর্তৃক পরমাণু-বিদীর্ণ]
ঠিকই শুনেছি; কিন্তু একটিমাত্র পরমাণুর ওজন (ভর) বা ‘m’ কতটুকু হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন হচ্ছে 166 x 10^-24 গ্রাম ব্যাপারটা আমরা ধারণাই করতে পারি না। আসুন, একটা তুলনামূলক বিচার করি : একবিন্দু জলের তুলনায় জলকণার একটি অণু (molecule) হচ্ছে এই তেরো হাজার কিলোমিটার ব্যাস-বিশিষ্ট পৃথিবীর তুলনায় একটি পিংপঙের বল!! বলা বাহুল্য, পরমাণু হচ্ছে ওই অণুর ভগ্নাংশ। ফলে একটিমাত্র পরমাণুর বিলোপে যেটুকু শক্তি উৎপাদন হল তা অতি সামান্যই।
.
০৫.
রাম-দুই-তিন-চার-পাঁচ! হাঁটি-হাঁটি পা-পা। পরমাণু-বোমা খেলাঘরের দিকে পাঁচটি পদক্ষেপ এগিয়েছে বিশবছরে। 1919 থেকে 1938-এর মধ্যে। এক-নম্বর, লর্ড রাদারফোর্ডের পোটন-সন্ধান এবং মৌলপদার্থের ট্রান্সমুটেশন। দু-নম্বর, চ্যাডউইকের নিউট্রন-আবিষ্কার, তিন-নম্বর, জোলিও-কুরির বীক্ষণাগারে আলাদিনের আশ্চর্য-প্রদীপ থেকে সদ্যোমুক্ত নিউট্রন, চার-নম্বর, ফের্মির অজ্ঞাতসারে ইউরেনিয়াম পরমাণুর হৃদয়-বিদীর্ণকরণ এবং পাঁচ নম্বর ধাপ, প্রফেসর অটো হান-এর সজ্ঞান ব্যাখ্যা! অথচ আশ্চর্য! পাঁচ-পাঁচটা ধাপ অতিক্রম করেও সে-যুগের বিজ্ঞানীরা ভাবতে পারছেন না, এই পরীক্ষাবলীর শেষ ফলশ্রুতি : অ্যাটম-বোমা! প্রমাণ? দিচ্ছি :
1939-এর জানুয়ারিতে বিশ্ববিজ্ঞানের তিন-তিনজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের বক্তব্য শুনুন।
প্রফেসর নীলস বোহর তার সহকারী উইগনারকে বলছেন, “পরমাণুর ভিতরকার ওই অপরিসীম সুপ্তশক্তিকে মানুষ কোনোদিনই কাজে লাগাতে পারবে না। অন্তত পনেরোটি অনতিক্রম্য বাধা আমার নজরে পড়েছে।”
প্রফেসর অটো হান তার সহকর্মী কোর্সচিংকে ওই সময় বলেছেন, “পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তিকে মানুষ কুক্ষিগত করুক এটা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়–তাই আমাদের সামনে তিনি রেখেছেন অসংখ্য অনতিক্রম্য বাধা।”
প্রফেসর অ্যালবার্ট আইনস্টাইন একই সময়ে আমেরিকান রিপোর্টার ডাবলু এল লরেন্সকে বলছেন, “পরমাণুর ভিতরের ঘুমন্ত শক্তিকে মানুষের কাজে লাগানো কোনোদিনই হয়তো সম্ভবপর হবে না, অন্তত আমাদের জীবদ্দশায় নয়।”
***
এ-যুগের ইতিহাস আমি খুঁটিয়ে দেখেছি; দেখেছি–একজন বিজ্ঞানী সেই সময় থেকেই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। আমি হাঙ্গেরিয়ান বিজ্ঞানী ৎজিলাৰ্ড এর কথা বলছি।
ইতিমধ্যে ভিয়েনা থেকে ৎজিলাৰ্ড এসেছেন ইংল্যান্ডে। সেখান থেকে মার্কিনমুলুকে। এখানে এসে কোনো চাকরি-বাকরি তখনও ধরতে পারেননি; কিন্তু কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাকে ল্যাবরেটারিতে কাজ করবার সুযোগ দিয়েছিলেন। অটো হান-এর প্রবন্ধ পড়ে তার মনে পড়ে গেলো সেই ছয় বছর আগেকার কথা। লর্ড রাদারফোর্ড-এর বক্তৃতা শুনে সেদিন তার যা মনে হয়েছিল তার কথা। ৎজিলাৰ্ড তার বন্ধু লিবোউইজ-এর কাছ থেকে দু হাজার ডলার ধার নিলেন এবং এক গ্রাম রেডিয়াম কিনে কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা শুরু করে দিলেন! তিন-চার দিন পরে তাঁর পরীক্ষার ফলাফলগুলি দেখে নিরতিশয় আতঙ্কিত হলেন তিনি। তার মনে হল–রেডিয়াম বা ইউরেনিয়ামের পরমাণুকে বিদীর্ণ করে ইতিমধ্যেই একটি নিউট্রনকে মুক্ত করা গেছে। যদি ওই ধাতুর পরিমাণ কিছু বেশি হয়, এবং এমন ব্যবস্থা করা যায় যাতে একের-পর-এক নিউট্রন মুক্ত হবে–তাহলে ‘চক্রাবর্তন অবস্থা’ অর্থাৎ ‘চেন রিয়্যাকশান’ শুরু হবে যাবে। তার অনিবার্য ফল অত্যন্ত শক্তিশালী এক বিস্ফোরক। তাতে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যেতে পারে!
ৎজিলাৰ্ড এসে হাজির হলেন পোপের দরবারে–ফিজিক্স-এর পোপ, এনরিকো ফের্মি!
ফের্মি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন ফ্যাসিস্ট ইটালির জীবনযাত্রায়। নাৎসি জার্মানির মতো সেখানেও বৈজ্ঞানিকদের ওপর কর্তৃত্ব করছিল মুসোলিনির গুপ্তচর বাহিনী। বিজ্ঞানভিক্ষু ফের্মি পালাবার পথ খুঁজছিলেন। সুযোগ হয়ে গেলো হঠাৎ তিনি নোবেল-প্রাইজ পেয়ে বসায়। 1938এ ফের্মিকে সুইডেন থেকে আমন্ত্রণ করা হল। সস্ত্রীক ফের্মি এলেন স্টকহমে। প্রাইজ নিলেন, কিন্তু ইটালিতে ফিরলেন না আর। সোজা পাড়ি জমালেন আমেরিকায়। এখন তিনি আমেরিকায়।
ফের্মিকে ৎজিলাৰ্ড সব কথা খুলে বললেন। বললেন, আমি বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে একমত নই। আমার ধারণা–পরমাণু-বোমা আদৌ অসম্ভব নয়। যেমন করে হোক এ দুর্দৈবকে রুখতে হবে।
ফের্মি বলেন, বেশ মানলাম। কিন্তু কেমন করে সেটা রুখবেন আপনি?
–আমার ধারণা–এ পৃথিবীতে আজ বারোজন–মাত্র বারোজন বৈজ্ঞানিক–এই অসম্ভবকে সম্ভব করতে সক্ষম। আপনি সেই বারোজনের একজন। তাই আপনার কাছেই প্রথম এসেছি।
–ঠিক কী বলতে চাইছেন?
–এই বারোজন বৈজ্ঞানিক যদি প্রতিজ্ঞা করেন–তাদের আবিষ্কারের কথা বাইরের দুনিয়াকে জানতে দেবেন না–অন্তত ওই যেসব লোক ব্রাস-হেলমেট পরে ছড়ি ঘুরিয়ে বেড়ায়, তাদের জানতে দেবেন না, তাহলেই কাজ হবে।
ফের্মি গম্ভীর হয়ে বলেন, হের ৎজিলাৰ্ড! ওই বারোজনের মধ্যে বেশ কয়েকজন আছেন জার্মানিতে–অটো হান, হেইসেনবের্গ, ফন লে ইত্যাদি। নয় কি? নাৎসি জার্মানি কি তাদের রেহাই দেবে?
–কিন্তু কিছু তো করা দরকার! আপনিই অগ্রণী হন!
-বেশ। আগামী শনিবার আমার এখানে আরও কয়েকজনকে ডাকছি। সবাই মিলে পরামর্শ করে দেখা যাক।
***
কদিন পরে এনরিকো ফের্মির বাড়িতে বসল একটা ঘরোয়া বৈঠক। ফের্মি আর ৎজিলাৰ্ড ছাড়া সেখানে ছিলেন আরও তিনজন তরুণ বিজ্ঞানী। উইগনার, টেলার আর গ্যামো। ওঁদের সামনে ৎজিলাৰ্ড তাঁর বক্তব্য রাখলেন, বললেন
একটা কথা আপনারা খুব ধীর-স্থিরভাবে ভেবে দেখুন। হিটলার লোকটা পাগল নয়, তাহলে সে কোন্ সাহসে সারা দুনিয়ার বিরুদ্ধে দ্বৈরথ সমরে নামতে চায়? হা, সারা দুনিয়া! একমাত্র মুসোলিনি আর জাপান ছাড়া সে কারও সঙ্গে সদ্ভাব রাখার চেষ্টা করছে না। আমরা জানি, জার্মানির সমর-সম্ভার অনেক বেশি, অনেক উন্নত। তার এয়ারক্রাফট, তার ট্যাঙ্ক, সাবমেরিন তার শত্রুদের চেয়ে সংখ্যায় বেশি এবং অনেক বেশি কার্যকরী। কিন্তু এ কথাও তো নির্মম সত্য যে, তার শত্রুদের তুলনায় তার জনবল, খনিজসম্পদ, খাদ্য-সম্ভার অনেক কম। বিশ্বযুদ্ধে যে রাতারাতি জেতা যায় না–সেটা তো প্রথম বিশ্বযুদ্ধেই জার্মানি হাড়ে-হাড়ে বুঝেছে। তাহলে এই ইকোয়েশানে কী এমন অজ্ঞাত ফ্যাকটার ‘X’ আছে যাতে সমীকরণের পাল্লা ভারী হয়ে পড়ছে?
টেলার বলেন, আপনিই বলুন।
ৎজিলাৰ্ড তৎক্ষণাৎ টেবিলের ওপর মেলে ধৰেন একটা জার্মান পত্রিকা Deutsche Allegemeine Zeitung। তাতে প্রকাশিত হয়েছে ডক্টর ফুগ-এর একটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধপাঠে জানা গেলো, তিরিশে এপ্রিল 1938-এ বার্লিনে ছয়জন জার্মান নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট সম্মিলিত হয়েছিলেন সরকারি উদ্যোগে–উদ্দেশ্য পরমাণুশক্তির সন্ধান! ওঁরা কতদূর কী করছেন তাও কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছে।
ৎজিলাৰ্ড বললেন, মন্ত্রগুপ্তি নাৎসি জার্মানির ধর্ম। তারা যখন প্রকাশ্যে এতকথা লিখেছে তখন নিশ্চয়ই তারা গোপনে অনেক অনেকটা এগিয়ে আছে। হয়তো। বছরখানেকের ভিতরেই ওরা পরমাণু-বোমা তৈরি করে ফেলবে। আমার দৃঢ় ধারণা এই পরমাণু-বোমাটিই হচ্ছে আমাদের ওই সমীকরণের যাথার্থ্য বিষয়ে অজ্ঞাত রহস্য X! ওই শক্তির জন্যই হিটলার এতটা বেপরোয়া!
ফের্মি বললেন, ধরা যাক আপনি যা বললেন তাই সত্য। এ-ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী?
ৎজিলাৰ্ড বলেন, আমার মতে দুটি কাজ অবিলম্বে আমাদের করা উচিত। প্রথম কাজ হচ্ছে, নাৎসি জার্মানি এবং ফ্যাসিস্ট ইটালির বাইরে যেসব বিজ্ঞানী আছেন তাদের একতাবদ্ধ করা। তাদের প্রতিজ্ঞা করানো–যা কিছু আবিষ্কার তারা করছেন তা কাগজে প্রকাশ করবেন না–নিজেদের মধ্যেই গোপন রাখবেন। দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে, জার্মানিতে আমাদের যেসব বন্ধু আছেন তাদের মাধ্যমে জানবার চেষ্টা করা–ওরা কতদূর কী করেছে।
ইতিমধ্যে ফ্রাই ফের্মি মদের বোতল আর ডিক্যানটার রেখে গিয়েছিলেন টেবিল-এ। ফের্মি তার পানপাত্রটা হাতে তুলে নিয়ে বললেন, আমাকে মাপ করবেন ডক্টর ৎজিলাৰ্ড। আমি আপনার দুটি প্রস্তাবের একটাও খুশি মনে মেনে নিতে পারছি না।
-কেন?
–আপনার প্রথম প্রস্তাব হচ্ছে, বিজ্ঞানীরা তাদের ল্যাবরেটারির ওপর স্বপ্রযুক্ত সেনসর বসাবেন। গোপনীয়তা অবলম্বন করবেন। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য–আমি সদ্য ফ্যাসিস্ট ইটালি থেকে পালিয়ে এসেছি। ওইসব গোপনীয়তা আর সেনসারের হাত এড়াতে। বিজ্ঞানমন্দিরের দ্বারে ওরা বেয়নেটধারী সৈনিক বসিয়েছিল বলেই দেশত্যাগ করেছি। আমেরিকায় এসে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছি। সুতরাং আবার ওফাঁদে আমি পা দেব না।
একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল ৎজিলাৰ্ড-এর। কী বলবেন, ভেবে পেলেন না।
–আপনার দ্বিতীয় প্রস্তাব হচ্ছে–আমরা গোপনে সংবাদ সংগ্রহ করবার চেষ্টা করব–জানতে চাইব, জার্মানিতে কী হচ্ছে না হচ্ছে। তাতেও আমার ঘোরতর আপত্তি। ও কাজ প্রচরের বিজ্ঞানভির নয়। অন্তত আমি ওতে নেই!
উইগনার বলেন, তাহলে আমার বিকল্প প্রস্তাবটা শুনুন। আমি মনে করি, এক্ষেত্রে আমাদের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে, যে-দেশ আমাদের মতো বাস্তুচ্যুত বৈজ্ঞাকিদের আশ্রয় দিয়েছে সেই দেশের সরকারকে এবিষয়ে অবহিত করা। ব্যাপারটার গুরুত্ব ও বিপদ সম্বন্ধে মার্কিন সরকারকে সতর্ক করার সময় হয়েছে।
সকলেই একবাক্যে এ প্রস্তাব মেনে নিলেন। এমন কি ফের্মিও।
কিন্তু কী করে কী করা যায়? ওঁরা পাঁচজনেই বিদেশি, মার্কিন নাগরিক নন। সদ্য এসেছেন। তাছাড়া একমাত্র ফের্মি আর ৎজিলাৰ্ড ছাড়া আর তিনজনই তরুণ এবং তখনও প্রথিতযশা নন। তবু চেষ্টা করে দেখলেন ওঁরা। একদিন ওঁরা গিয়ে সাক্ষাৎ করলেন নৌ-বাহিনীর অ্যাডমিরাল হুপার-এর সঙ্গে। ধৈর্য ধরে অ্যাডমিরাল হুপার ওই নোবেল-লরিয়েটদের বক্তব্য শুনলেন, কফি খাওয়ালেন, শ্যাম্পেন খাওয়ালেন এবং দ্বার পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেলেন। ওঁরা চলে আসতেই তিনি মনে মনে বললেন–পাগলগুলো অনেকটা সময় নষ্ট করে দিয়ে গেলো!
***
সেই মাসেই–এপ্রিলে, নিউইয়র্ক টাইমস-এ এক প্রবন্ধে নীলস বোহর লিখলেন, ‘নিউট্রনের আঘাতে ইউরেনিয়াম-পরমাণুতে এমন বিস্ফোরক উদ্ভাবিত হতে পারে যাতে এই গোটা শহরটা ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।‘
তাও মার্কিন কর্তৃপক্ষের কাউকে উদ্বিগ্ন করল না।
নিতান্ত ঘটনাচক্রেই বলতে হবে, এই সময়ে জার্মান পদার্থবিজ্ঞানী হেইসেনবের্গ আমেরিকায় এলেন কয়েক সপ্তাহের জন্য। ফের্মি তৎক্ষণাৎ দ্বারস্থ হলেন কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের। তিনি জানতেন, ৎজিলাৰ্ড-বর্ণিত দ্বাদশজন বিজ্ঞানীর মধ্যে হেইসেনবের্গ নিঃসন্দেহে একজন। তাকে আটকাতে হবে। আমেরিকাতেই।
অ্যাটম-বোমা ঠেকাতে নয়, অত্যন্ত প্রতিভাশালী বৈজ্ঞানিককে নিয়োগ করতে স্বতই উৎসাহিত হলেন কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। হেইসেনবের্গকে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদ অফার করা হল। কিন্তু সবিনয়ে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন হেইসেনবের্গ। ঘরোয়া পরিবেশে একদিন তাকে পাকড়াও করলেন ফের্মি আর ৎজিলাৰ্ড। ফের্মি সরাসরি প্রশ্ন করে বসলেন, হের প্রফেসর, আপনাকে একটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব? কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদটা আপনি নিলেন না কেন?
কৌতুক উপছে পড়ল তরুণ অধ্যাপকের দু-চোখ থেকে। পঁচিশ বছর বয়সে নোবেল-প্রাইজ পাওয়ার মতো থিসিস যিনি লিখেছিলেন। বললেন, ব্যক্তিগত প্রশ্নের জবাব : যে জন্য আপনারা আমাকে আটকাতে চাইছেন তার প্রয়োজন নেই। হিটলার এ যুদ্ধে হারবে! কিন্তু সেজন্য আমি তো আমার পিতৃভূমিকে ত্যাগ করতে পারি না। সে দুর্দিনে আমাকে থাকতে হবে সেই পরাজিত জার্মানিতেই। ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে থেকে জার্মানির যা কিছু মহান সম্পদ তাকে রক্ষা করতে হবে আমাদেরই।
ফের্মি জবাব দিতে পারেননি। তিনি ইটালিকে অনিবার্য ধ্বংসস্তূপের মাঝখানে ফেলে রেখে এসেছেন!
ৎজিলাৰ্ড কিন্তু থাকতে পারেন না। পুনরায় প্রশ্ন করলেন–প্রফেসর! অটো হান-এর পরীক্ষা বিষয়ে আপনার কী অভিমত? ইউরেনিয়াম পরমাণুর ভিতর চেন-রিয়াকশান কি সম্ভব?
হেইসেনবের্গ বলেছিলেন, আমি তো তাই মনে করি। এ দুনিয়ায় আজ দশ-বারোজন বৈজ্ঞানিক আছেন যাঁরা মিলিতভাবে চেষ্টা করলে এটাকে বাস্তবায়িত করতে পারেন।
ৎজিলাৰ্ড উৎসাহিত হয়ে বলেন, ঠিক কথা। এবং সেই দশ-বারোজন বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে আছেন আপনারা দুজন–আপনি আর প্রফেসর ফের্মি।
হেইসেনবের্গ মৃদু হাসলেন; জবাব দিলেন না।
ৎজিলাৰ্ড পুনরায় বলেন, হের প্রফেসর! সেই চেন-রিয়্যাকশান এমন বিস্ফোরকের জন্ম দিতে পারে–যাতে পৃথিবীর ধ্বংস হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে, তাই নয়?
হেইসেনবের্গ মাথা নেড়ে সায় দিলেন।
–তাহলে এই মুষ্টিমেয় দশ-বারোজন বৈজ্ঞানিক কি একযোগে এই পৃথিবীটাকে সেই অভিশাপ থেকে বাঁচাতে পারেন না?
–পারেন! থিয়োরেটিক্যালি! কিন্তু সে সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করার কোনো পথ তো আমি দেখছি না! আপনারা যদি পারেন, আমি খুশি হব।
***
ৎজিলাৰ্ড কিন্তু অত হতাশ হলেন না। ইতিমধ্যে ফের্মিও মত বদলেছেন। তিনিও ৎজিলাৰ্ড-এর সঙ্গে একমত হয়েছেন–অতঃপর বিশ্বের সব নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট-এর উচিত তাদের পরীক্ষার ফলাফল গোপন রাখা। ৎজিলাৰ্ড স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সব কয়টি বৈজ্ঞানিককে তার প্রস্তাব পাঠালেন। ডেনমার্ক, কেমব্রিজে, পারিতে। কিন্তু তার একক প্রচেষ্টায় কোনো কিছুই হল না। স্বতঃপ্রযুক্ত গোপনীয়তার যুক্তি কেউই মেনে নিলেন না। এর প্রয়োজনটাই সেদিন মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারেননি কেউ।
এদিকে মার্কিন নৌ-বহরে বড়সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ওঁরা বুঝলেন, এভাবে কর্তৃপক্ষের টনক নড়বে না। ফের্মি-ৎৎজিলাৰ্ড-উইগনার-টেলার এবং গ্যামো সান্ধ্য-আসরে এ নিয়ে প্রায়ই আলোচনা করতেন–কীভাবে মার্কিন বড়কর্তাদের সমস্যাটার বিষয়ে অবহিত করা যায়।
শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি যোগাল ওই লিও ৎজিলাৰ্ড-এর মাথাতেই। ব্যাপারটা প্রফেসর আইনস্টাইনকে জানালে কেমন হয়? তিনি যদি বড়কর্তাদের কাউকে চিঠি লিখতে রাজি হন তবে কাজ হতে পারে। আইনস্টাইন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। তার চিঠিকে উপেক্ষা করবে না কেউ। ধরা যাক, তিনি লিখলেন যুদ্ধসচিব স্বয়ং হেনরি স্টিমসনকে।
-না! হেনরি স্টিমসন নয়–বললেন, এনরিকো ফের্মি–প্রফেসর আইনস্টাইন যদি আদৌ কোনো চিঠি লেখেন তবে লিখবেন সরাসরি F. D. R.-কে!
ঠিক কথা! যুদ্ধসচিব, প্রধান সেনাপতি-উতি নয়–স্বয়ং রুজভেল্টকে!
যে কথা সেই কাজ। ইউজিন উইগনার আর লিও ৎজিলাৰ্ড একদিন জুলাই মাসের এক রৌদ্রতপ্ত দিনে গাড়িটা নিয়ে রওনা হয়ে পড়লেন লং-আইল্যান্ডের দক্ষিণতম প্রান্তে এক ছোট্ট জনপদের উদ্দেশ্যে–তার নাম Patchogue। সেখানেই নাকি বাস করেন অ্যালবার্ট আইনস্টাইন।
সঠিক পাত্তাটা জানা ছিল না। সারাটা দিন ঘুরে মরলেন ওঁরা। ‘প্যাঁচক’ গ্রাম কোথায় কেউ বলতেই পারে না। প্যাঁচক না পেকনিক? পেকনিক বলে একটা গ্রাম আছে আরও দক্ষিণে। শেষ পর্যন্ত হয়রান হয়ে উইগনার বললে : লিও, আমার মনে হচ্ছে এটাই দৈবের নির্দেশ। প্রফেসর আইনস্টাইন চিরকাল রাজনীতি থেকে দূরে থেকেছেন। তাই বোধহয় ঈশ্বর আমাদের এভাবে পথভ্রান্ত করছেন। হয়তো এই ভালো হল। প্রফেসর আইনস্টাইনের সই করা কোনো চিঠি কেউ ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেললে আমি কোনোদিন নিজেকে ক্ষমা করতে পারতাম না।
ৎজিলাৰ্ড স্টিয়ারিঙে একটা হাত রেখে বলেন, অতটা সেন্টিমেন্টাল হয়ো না বন্ধু! আমাদের দুজনের হাতে হয়তো এই মুহূর্তে নির্ভর করছে গোটা মানবসভ্যতার নিরাপত্তা। এত সহজে হতাশ হলে আমাদের চলে?
যেন ৎজিলাৰ্ডই কম সেন্টিমেন্টাল!
উইগনার বলেন, একটা কথা লিও। আমরা এতক্ষণ প্যাঁচক গ্রামের খোঁজ করেছি। তার চেয়ে বরং লোকজনকে জিজ্ঞাসা করি না কেন, আইনস্টাইন কোথায় থাকেন?
-ঠিক কথা! একটা বাচ্চা ছেলেও আইনস্টাইনের নাম জানে!
–ওই তো একটা বাচ্চা ছেলে! এসো। ওকে দিয়েই শুরু করি।
দুই বন্ধু নেহাৎ কৌতুকের ছলে এগিয়ে গেলেন বাচ্চাটার দিকে। বছর-সাতেক বয়স তার। বাড়ির রোয়াকে বসে একটা কুকুরছানাকে আদর করছিল।
ৎজিলাৰ্ড বলেন, খোকা! তুমি আইনস্টাইনের নাম শুনেছ?
–নিশ্চয় শুনেছি। কেন, তোমরা শোননি?
থতমত খেয়ে ৎজিলাৰ্ড বলেন, না মানে,..তার বাড়িটা কোথায় জান?
নিশ্চয় জানি। কেন, তোমরা জান না?–ওই তো ওই বাড়িটা।
বস্তুত যেখানে গাড়ি থামিয়ে উইগনার বলছিলেন–ভাগ্যদেবতার নির্দেশ অন্যরকম, সেখানে থেকে কথার বদলে ঢিল ছুঁড়লে আইনস্টাইনের বৈঠকখানার জানলার কাঁচ ভেঙে যেত!
***
এ বর্ণনা আমি সঙ্কলন করেছি লিও ৎজিলার্ডের স্মৃতিচারণ থেকে। এবার তার ইংরেজি রচনার একটি মূল পংক্তি উদ্ধার করে দিচ্ছি। পাছে অনুবাদ করতে গিয়ে তার অঙ্গহানি করে বসি–
The possibility of a chain reaction in Uranium had not oc curred to Einstein. But almost as soon as I began to tell him about it, he realized what the consequences might be and immediately signifed his readiness to help us and, if necessary, to ‘stick out his neck’. as the saying goes.
এমন অদ্ভুত মানুষ ছিলেন আলবার্ট আইনস্টাইন। ইউরেনিয়াম-এর চেন রিয়াকশানের কথা কখনও তার মনে হয়নি–তিনি ছিলেন অন্য জগতে; সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় ব্যস্ত। ইউনিফায়েড ফিল্ড থিওরি’র (একীভূত ক্ষেত্র তত্ত্ব) মাধ্যমে পদার্থবিদ্যার সর্ব-সমস্যা-সমাধানের চিন্তাতেই ছিলেন বিভোর; কিন্তু দুটি তরুণ বৈজ্ঞানিক মুখ খুলবার আগেই তিনি বুঝে নিলেন ওঁরা কী বলতে চান, কেন বলতে চান, এবং কী তার প্রতিকার!
সপ্তাহখানেক পরে ৎজিলাৰ্ড আবার ফিরে এলেন আইনস্টাইনের নির্জন আবাসে। এবার তার সঙ্গী এডওয়ার্ড টেলার। সঙ্গে দুখানি চিঠির ড্রাফট। একটি সংক্ষিপ্ত পত্র, একটি বিস্তারিত। প্রফেসর আইনস্টাইন দুটি চিঠিই পড়ে দেখলেন। দীর্ঘতর পত্রটিই অনুমোদন করলেন তিনি। সই দিলেন তাতে।
পৃথিবীর ইতিহাসে এই পত্রখানির একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। আওরঙ্গজীবকে লেখা রাজসিংহের পত্রের মতো, বড়লাটকে লেখা রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণার মতো এ চিঠিখানিও (পরিশিষ্ট ঘ) বিশ্ব-ইতিহাসের সম্পদ। তাই আরও বলি–চিঠিখানির বয়ানে মতদ্বৈধ আছে। স্বয়ং আইনস্টাইন বলেছেন, “আমি শুধু সই দিয়েছিলাম টাইপ করা চিঠির নীচে। দায়-দায়িত্ব আমার, কিন্তু রচনা আমার নয়। বলেছিলেন অনেক পরে তার জীবনীকার ভ্যালেনটিনকে। অপরপক্ষে ৎজিলাৰ্ড বলেছেন, আমার যতদূর মনে পড়ে প্রফেসর আইনস্টাইন জার্মান ভাষায় ডিকটেশান দেন এবং টেলার সেটা শর্টহ্যান্ডে লিখে নেন। সেইটা অবলম্বন করে আমি দুখানি চিঠি ইংরেজিতে রচনা করি–একটা হ্রস্ব, একটা দীর্ঘ। প্রফেসর নিজেই তার ভিতর থেকে বৃহত্তরখানি বেছে নেন! পত্রের অনুষঙ্গ হিসাবে আমি একটি মেমোরান্ডাম যুক্ত করে দিই।
চিঠিখানি ডাকে পাঠালে যথোপযুক্ত ফলপ্রসূ হবে না। এমন কারও হাতে পাঠাতে হবে যিনি পাঁচ-কাজে-ব্যস্ত প্রেসিডেন্টকে বুঝিয়ে দিতে পারেন। ডক্টর আলেকজান্ডার সাক্স একজন কোটিপতি–প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের বন্ধুস্থানীয়। হোয়াইট হাউসে যাতায়াত আছে তার! সব কথা শুনে তিনি দায়িত্ব নিলেন। চিঠিখানি প্রেসিডেন্টকে পৌঁছে দেবেন এবং তার গুরুত্ব সম্বন্ধে প্রেসিডেন্টকে অবহিত করবেন। সাস ইন্টারভিউ চাইলেন; কিন্তু সেটা পেতেই তাঁর সময় লাগল আড়াই মাস। আগস্টের প্রথম সপ্তাহে আইনস্টাইন যে চিঠির নীচে সই দেন সেটি নিয়ে তিনি হোয়াইট হাউসে হাজির হলেন এগারোই অক্টোবর 1939। অর্থাৎ ইউরোপখণ্ডে ততদিনে বিশ্বযুদ্ধের বয়স একমাস। আমেরিকা তখনও নিরপেক্ষ। দীর্ঘ পত্রটি নিজেই পড়ে শোনালেন সাক। বেশ বুঝতে পারছিলেন, তার শ্রোতা উসখুশ করছেন। ভদ্রতায় বাধছে বলে নয়, আইনস্টাইনের মতো বৈজ্ঞানিককে অসম্মান দেখানো হবে বলে ওঁকে মাঝপথে থামিয়ে দিচ্ছেন না। সে যাই হোক, পত্রপাঠ একসময়ে শেষ হল। প্রেসিডেন্ট মামুলি ধন্যবাদ জানিয়ে সাসকে বললেন, চিঠিখানি বেশ ইন্টারেস্টিং, তবে এ বিষয়ে সরকারি তরফে এখনই কিছু করতে যাওয়া সম্ভবপর নয়। যাহোক, আমি ভেবে দেখব।
ৎজিলাৰ্ড, ফের্মি, টেলার প্রভৃতি যে আশঙ্কা করেছিলেন, তাই বাস্তবে হতে বসেছে দেখে সাক্স চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন। বলেন, আমার আরও কয়েকটি কথা বলার ছিল।
প্রেসিডেন্ট ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। এখন আর আমার সময় হবে না।
-তাহলে আবার কবে আসব?
একটু থতমত করে প্রেসিডেন্ট বলেন, আচ্ছা কাল সকালে আসুন। সাতটায়।
***
আলেকজান্ডার সাকস লিখছেন, “সে রাত্রে আমি একটি মুহূর্তের জন্যেও ঘুমাতে পারিনি। আমি ছিলাম কার্লটন হোটেলে। সারারাত ঘরের ভিতর পায়চারি করেছি। বেশ বুঝতে পারছি, রাত্রি প্রভাতেও অত্যন্ত অল্প সময় পাব–বড়জোর পাঁচ-সাত মিনিট। ওর ভিতরেই কেমন করে কার্যসিদ্ধি সম্ভব? এমন কিছু বলতে হবে যা চরম নাটকীয়, যা মর্মমূলে গিয়ে বিধবে প্রেসিডেন্টের। চমকে উঠবেন উনি। ঔদাসীন্য মুছে যাবে মুহূর্তে। কিন্তু কী সেই নাটকীয় ভাষণ? শেষে হোটেল ছেড়ে আমি সামনের পার্কটায় চলে গেলাম। বেশ মনে আছে, দারোয়ান অবাক হয়ে গেল–কারণ রাত তখন তিনটে। পার্কের বেঞ্চে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ আমার মাথায় একটা ফন্দি খেলে গেলো! হ্যাঁ-হলে, ওই অস্ত্রেই প্রেসিডেন্ট কাৎ হবেন!
“আমি ফিরে এলাম হোটেলে। স্নান করলাম। ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে ছটা। হোয়াইট হাউসে টেলিফোন করলাম। ওঁর সেক্রেটারি জানালো ব্রেকফাস্ট টেবিলে প্রেসিডেন্ট আমার জন্যে সকাল সাতটায় অপেক্ষা করবেন। তৎক্ষণাৎ রওনা হয়ে। পড়লাম আমি।
“খানাকামরায় একাই বসেছিলেন প্রেসিডেন্ট। তার চাকা-দেওয়া চেয়ারে। আমাকে দেখেই বলেন, বসুন! ব্রেকফাস্ট এমনিতেই বেশি খাওয়া হয়েছে–তার ওপর আপনার গুরুপাক বক্তৃতাটা হজম হবে তো?
“উনি আমার সঙ্গে এমন রসিকতা করতেন মাঝে মাঝে। আমার মন কিন্তু সেদিন রসিকতার জন্য প্রস্তুত ছিল না! জবাবে আমি গম্ভীরভাবে বললাম, আমি আপনার বেশি সময় নেব না। যা বলবার তা প্রফেসর আইনস্টাইন বলেছেন। তার অনুষঙ্গ হিসাবে প্রায় দেড়শো বছর আগেকার (1805) একটা ছোটো গল্প আমার মনে পড়ে গিয়েছিল-গল্প নয়, সত্য ঘটনা। আমার মনে হল, সেটা আপনাকে বলে রাখা ভালো।
“প্রেসিডেন্ট পুনরায় ঠাট্টা করে ওঠেন, ও! বক্তৃতা নয়, গপ্পো! বলুন, বলুন, আমার প্রচুর সময় হাতে আছে।”
“আমি বলে চলি–নেপোলিয় বোনাপার্ট তখন গোটা ইউরোপের মালিক। বাকি আছে শুধু ইংল্যান্ড। ট্রাফালগার যুদ্ধের ঠিক আগের কথা। রবার্ট ফুলটন নামে একজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক এসে দেখা করল বিশ্বজয়ী নেপোলিয়র সঙ্গে। নেপোলিয় তখন অত্যন্ত ব্যস্ত। ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে ইংল্যান্ড আক্রমণের যাবতীয় ব্যবস্থা করতে হচ্ছে তাকে। ওই বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে কথা বলার সময় নেই। আড়াই মাস চেষ্টা করে শেষমেশ বৈজ্ঞানিক মাত্র কয়েক মিনিটের সময় পেলেন সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের। তার ভিতরে তিনি কোনোক্রমে বললেন, তিনি এমন এক ধরনের জাহাজ প্রস্তুত করতে পারেন, যা নাকি পালের হাওয়ায় চলে না, চলে বাষ্পের শক্তিতে! নেপোলিয় ওঁর কথা শুনে মনে মনে হেসেছিলেন। পাল-ছাড়া শুধু বাষ্পে জাহাজ চলতে পারে এমন আষাঢ়ে গল্পটা তিনি বিশ্বাসই করতে পারেননি। তবু সৌজন্যবোধে বলেছিলেন, আপনার পরিকল্পনাটা বেশ ইন্টারেস্টিং। আচ্ছা, ভেবে দেখব আমি!
“আমি গল্প শেষ করলাম। দেখি প্রেসিডেন্টের মুখটা থমথম করছে।”
“পুনরায় বলি, সেদিন যদি নেপোলিয় আর একটু দূরদর্শিতার পরিচয় দিতেন, আর একটু সম্মান দেখাতেন বৈজ্ঞানিকটিকে তাহলে পৃথিবীর ইতিহাস হয়তো অন্যভাবে লেখা হত!
“আরও তিন-চার মিনিট নির্বাক বসে রইলেন রুজভেল্ট। প্রস্তরমূর্তির মতো। গভীর চিন্তায় মগ্ন। তারপর তিনি একটি কাগজে কী লিখে খানা-কামরার আর্দালির হাতে দিলেন। লোকটা ভিতরে গেল এবং ফিরে এল একটি মদের বোতল নিয়ে। নেপোলিয়ঁর সমসাময়িক ফরাসি কনিয়াক। দীর্ঘদিন সেটা রাখা ছিল রুজভেল্টের সেলারে। কী জানি কেন হঠাৎ এই মুহূর্তটিকে ‘সেলিব্রেট করতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট। দুশো বছরের পুরাতন মদ নিজে হাতে ঢাললেন দুটি পাত্রে। একটি বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে, অপরটি তুলে আমাকে ইঙ্গিত করলেন। আমার স্বাস্থ্যপান করে, পুরো পাঁচ মিনিট পরে নীরবতা ভেঙে রুজভেল্ট বললেন, ‘অ্যালেক্স? তুমি মোদ্দা যে কথাটা বলতে চাও তা তো এই : নাৎসিরা পরমাণুবোমায় আমাদের যেন উড়িয়ে না দেয়। কেমন তো?
“ঠিক তাই!”
“তৎক্ষণাৎ বেল বাজালেন প্রেসিডেন্ট। ডেকে পাঠালেন তার মিলিটারি অ্যাটাশে জেনারেল ‘পা’ ওয়াটসনকে। পরমুহূর্তে এসে উপস্থিত হলেন জেনারেল। সসম্মানে দাঁড়ালেন আদেশের অপেক্ষায়। আইনস্টাইনের কাছ থেকে পাওয়া চিঠির গোছা তার দিকে বাড়িয়ে ধরে প্রেসিডেন্ট শুধু বললেন একটি বাক্য :
“–পা! দিস রিকোয়্যার্স অ্যাকশন!”
৪. কী ৫-৯
০৬.
পা! দিস রিকোয়্যার্স অ্যাকশন!
ব্যাস। আর কিছু নয়। ইমিডিয়েট নয়, এমার্জেন্সি নয়, টপ-প্রায়োরিটি নয়, এমনকি টপ-সিক্রেটও নয়। কোনো বিশেষণের ভার নেই আদেশটায়। সাদামাটা হুকুম : পা! এটার ব্যবস্থা হওয়া দরকার।
তা হল। ব্যবস্থা হল। বিশেষণ-বিমুক্ত সেই আদেশের ‘অ্যাকশন’টার জাত নির্ণয় করব আমরা। তার অর্থনৈতিক মূল্য, গোপনীয়তা এবং ব্যাপকতা। প্রথমটায় কাজ শুরু হল ছোটো করেই। সারা মার্কিন মুলুকে দশটি রিসার্চ গ্রুপ এ নিয়ে গোপন গবেষণা শুরু করলেন। প্রথম বছরে অর্থ বরাদ্দ করা হল মাত্র তিন লক্ষ ডলার। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সেটা ব্যাপক আকার ধারণ করল। এক সময়ে বৈজ্ঞানিকের দল জানালেন, তামার চেয়ে রুপোর তারের বিদ্যুৎবাহী ক্ষমতা বেশি। তাদের কিছু রুপো চাই। টাকশালের আন্ডার-সেক্রেটারি ড্যানিয়েল বেল বললেন, বেশ, দেব। বলুন কতটা রুপো চাই?
মানহাটান প্রডাকশানের চিফ বললেন, ধরুন আপাতত পনেরো হাজার টন।
ড্যানিয়েল বেল আঁৎকে উঠে বলেন, টন! কী বলছেন মশাই। রুপোর ওজন কখনও টনে হয়? হয় আউন্সে!
মানহাটান চিফ লেসলি গ্রোভস্ জবাবে কিছু বলবার আগেই তার সহকারী বৈজ্ঞানিকটি বলেন, ঠিক আছে। তাই বলছি–ফাইভ পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন দু দ্য পাওয়ার এইট!’
ড্যানিয়েল বেল-এর মুখের নিম্নাংশ ঝুলে পড়ে। বলেন, তার মানে?
-পনেরো হাজার টন ইজুকালটু 5.4 x 10^8 আউন্স। আপনি আউন্সে জানতে চাইছিলেন তো? তাই বলছিলাম আর কি!
বেল তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, থাক স্যার, আর বিদ্যে জাহির করতে হবে না, ওই পনেরো হাজার টন রুপোই পাঠিয়ে দিচ্ছি।
আর গোপনীয়তা? রুজভেল্ট মারা যাবার পর হ্যারি ট্রুম্যান যখন এসে বসলেন তার শূন্য সিংহাসনে-চোদ্দই এপ্রিল 1945-এ-তখন তিনিও জানতেন না এতবড় মানহাটান প্রজেক্টের কথা। চেয়ারে বসার পরে তিনি সেটা শুনেছিলেন। তার চেয়েও মজার কথা হচ্ছে সেনেটের হ্যারি ট্রুম্যান 1940 সালে একটি কমিটির চেয়ারম্যানরূপে নির্বাচিত হন– ”কমিটি টু ইনভেস্টিগেট দ্য ন্যাশনাল ডিফেন্স প্রোগ্রাম”। যুদ্ধপ্রচেষ্টায় যে সরকারি অর্থ বিনিয়োগ করা হচ্ছে তার যাথার্থ্য নির্ণয় করে সেনেটকে জানানোর দায়িত্ব এই অনুসন্ধান কমিটির। তার চেয়ারম্যানরূপে কাজ করতে গিয়ে ট্রুম্যান জানতে পারলেন–কী একটা মানহাটান প্রজেক্টে কোটি কোটি ডলার ব্যয়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পে দৈনিক নাকি এক লক্ষ লোক খাটছে-ট্রেনে আর লরিতে লক্ষ লক্ষ টন কাঁচামাল ওই কারখানায় ঢুকছে, অথচ এ পর্যন্ত একটা ছোট্ট প্যাকেটও ‘ফিনিশড গুড় হিসাবে বার হয়ে আসেনি। ট্রুম্যান একটা প্রকাণ্ড কেলেঙ্কারী হাতেনাতে ধরবেন বলে ওই প্রকল্প সরেজমিনে দেখবার জন্য প্রস্তুত হলেন। খবর পেয়ে যুদ্ধসচিব বৃদ্ধ স্টিমসন সেনেটর হ্যারি ট্রুম্যানকে ফোন করলেন, বললেন, সেনেটর, আপনাকে একটি ব্যক্তিগত অনুরোধ জানাতে এসেছি। আপনি মানহাটান প্রজেক্ট সম্বন্ধে কোনো অনুসন্ধান করতে যাবেন না।
বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন সেনেটর হ্যারি ট্রুম্যান। বলেছিলেন, কেন মিস্টার সেক্রেটারি?
-কেন, তাও আমি বলতে পারব না। শুধু জানতে পারি, পৃথিবীর ইতিহাসে মানহাটান-প্রজেক্ট সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে গোপন প্রকল্প। এর পাই-পয়সা খরচের জন্য আমি যুদ্ধশেষে ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকব। আপনার অনুসন্ধান কার্য আমাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে দেবে।
প্রবীণ রাজনীতিক ওই সেক্রেটারি অফ ওয়ার-এর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল সেনেটর ট্রুম্যানের। তিনি তৎক্ষণাৎ অনুসন্ধানের আদেশ প্রত্যাহার করেছিলেন। তার পাঁচ বছর পরে ট্রুম্যান আমেরিকার প্রেসিডেন্টরূপে নির্বাচিত হন এবং তৎক্ষণাৎ তাকে আদ্যন্ত ব্যাপারটা খুলে বলেছিলেন যুগ্মসচিব হেনরি স্টিমসন! তার আগে নয়!
***
আর ব্যাপকতা? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্তে আট-দশটি বিভিন্ন কেন্দ্রে একযোগে চলছিল গবেষণা কার্য। কয়েক হাজার বৈজ্ঞানিক তাতে নিযুক্ত। 1942 সাল-ত বিজ্ঞানীরা পাঁচ-পাঁচটি বিকল্প পথে সমাধানের পথ খুঁজতে শুরু করেছেন। পাঁচটি পথের কোন্ পথ শেষ লক্ষ্যে পৌঁছাবে তা কেউ বলতে পারে না। তার ভিতর তিনটি পথ হচ্ছে ইউরেনিয়াম-বোমা তৈরি করবার প্রচেষ্টা, দুটি প্লুটোনিয়াম-বোমার।
বৈজ্ঞানিকেরা বলেছেন, ইউরেনিয়াম-বোমা তৈরির তিনটি বিকল্প পথ আছে। প্রথমত ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক উপায়ে। তার জন্য ভোলা হল দেশের দুই প্রান্তে দুই কেন্দ্র- বার্কলেতে এবং ওক-রিজে। দ্বিতীয় পথ–গ্যাসীয় ডিফুশন-মেথড। সে পরীক্ষাকার্য চালানো হল নিউইয়র্ক এবং ডেট্রয়েট-এ। তৃতীয় পথ হল–সেন্ট্রিফুজ-পদ্ধতি।
অনুরূপভাবে, প্লুটোনিয়াম-বোমা তৈরি হতে পারে দুটি পদ্ধতিতে-গ্রাফাইট রিয়্যাকটারে অথবা ভারী জল দিয়ে।
বস্তুত পাঁচটি অন্ধ গলিতেই তখন পথ হাড়াচ্ছেন বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকরা। পাঁচটি বিকল্প-পদ্ধতিতেই কোটি কোটি ডলার খরচ হচ্ছিল! কোনো পথই ওঁরা ত্যাগ করতে পারছিলেন না। কোটি অন্ধ গলি এবং কোন্ পথে লক্ষ্যে পৌঁছানেনা যাবে কেউ তা জানে না!
এই ফাঁকে বলে রাখি–আমাদের কাহিনির বিশ্বাসঘাতক ডেক্সটারের কল্যাণে রাশিয়া ওই পাঁচমাথার মোড়ে বিব্রত হয়নি–সোজা এক পথে এগিয়ে গিয়েছিল। তাতে কোটি কোটি রুল বেঁচে গিয়েছিল রাশিয়ার।
***
ম্যানহাটান-প্রকল্পের এক-এক প্রান্তে যারা কাজ করেন, তারা অপর প্রান্তের খবর জানেন না। গোপনীয়তার প্রয়োজনে নিজ ল্যাবরেটারির বাইরের খবর কেউ পান না। শুধু তাই নয়–প্রত্যেকে শুধু নিজ নিজ পরীক্ষার ফলাফলটুকুই জানতে পারেন, তার বেশি নয়। এ ব্যবস্থায় গোপনীয়তা রক্ষা হয় বটে কিন্তু কাজ দ্রুত এগোয় না। যে পরীক্ষার ফল চূড়ান্তভাবে জেনে ফেলেছেন ওক-রিজের বিজ্ঞানীরা সেগুলিই হয়তো কষে বার করছেন বার্কলের অধ্যাপকেরা। কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন–এভাবে চলবে না। সমগ্র ম্যানহাটান-প্রকল্পের একজন সর্বময় কর্তা চাই। নিঃসন্দেহে তিনি হবেন একজন সামরিক অফিসার। শুধু তাই নয়–চাই একজন প্রথম শ্রেণির অল্পবয়সী পদার্থবিজ্ঞানী, যিনি প্রতিটি কেন্দ্রের সংবাদ সংগ্রহ করে ওই সর্বময় কর্তাকে জানাবেন। এক কেন্দ্রের খবর অপর কেন্দ্রের প্রয়োজনবোধে জানাবেন।
যুদ্ধসচিবের নিজের কাজ অফুরন্তযুদ্ধের কাজ। সারা পৃথিবীতে মার্কিন সৈন্য তখন যুদ্ধ করছে। তাই এই মানহাটান প্রকল্পের জন্য তিনি একটি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সেট-আপ তৈরি করে দিলেন। তৈরি হল একটি উপদেষ্টা পরিষদ। তার চারজন সভ্য। যুদ্ধসচিবের পক্ষে রইলেন চিফ-অফ স্টাফ জেনারেল জর্জ মার্শাল। এঁদের পরামর্শ অনুসারে কাজ করবেন ওই সর্বময় কর্তা জেনারেল লেসলি গ্রোভ। তার মিলিটারি সহকারী রইলেন কর্নেল মার্শাল ও কর্নেল নিক। ছক তৈরি হল।
এই দশটি কেন্দ্রে যেসব বিজ্ঞানী কাজ করে গেছেন তাদের মধ্যে মুষ্টিমেয়ই সব কয়টি কেন্দ্রের খবর রাখতেন। কিন্তু মূল ভূমিকা ছিল দুজনের সামরিক কর্তা জেনারেল গ্রোভসস্ এবং বেসামরিক ডক্টর ওপেনহাইমারের। এঁদের দুজনকে আর একটু কাছ থেকে দেখতে হবে আমাদের।
***
1942 সালের সতেরোই সেপ্টেম্বর লেসলি গ্রোভসের জীবনে একটি স্মরণীয় দিন। সেদিনই সে বদলির অর্ডার পেলো। সাগরপারে যেতে হবে তাকে, আমেরিকার বাইরে। এই স্বপ্ন সে দেখে এসেছে আকৈশোর। গ্রোভস মিলিটারি স্কুল থেকে পাশ করে বের হয় 1918-তে। ঠিক সে বছরই যুদ্ধ শেষ হয়েছিল। ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশ নেবার সৌভাগ্য হয়নি বেচারার। তারপর এই দীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে একটাও যুদ্ধ করার সুযোগ সে পায়নি। অথচ ধাপে ধাপে ধীরে ধীরে উঠেছে ওপরে–এখন সে কর্নেল। এবারকার বিশ্বযুদ্ধে তার দায়িত্ব ছিল ‘মিলিটারি এঞ্জিনিয়ার যোদ্ধা!’ এতদিন পরে কর্নেল গ্রোভস বদলির অর্ডার পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বন্ধুদের দেখালো অর্ডারটা–এবার সে সাগরপারে সম্মুখ যুদ্ধক্ষেত্রে যাচ্ছে।
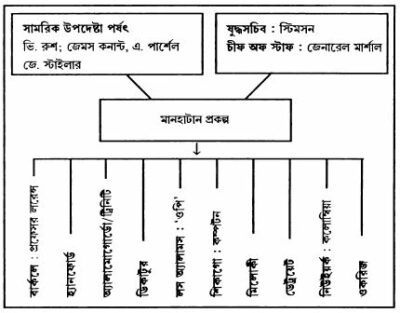
[চিত্র]
ধড়াচূড়া সেঁটে গ্রোভস এসে হাজির হল তার বড়কর্তার ঘরে। মেজর-জেনারেল সমারডেল ওকে সমাদর করে বসালেন। বললেন, অর্ডার পেয়েছ?
পেয়েছি জেনারেল, ধন্যবাদ। কখন আমি আমার বর্তমান কাজের দায়িত্ব। বুঝিয়ে দেব?
–এখনই। তোমার সাবস্টিট্যুট তৈরি আছে।
একটু ইতস্তত করে গ্রোভস বলে, কোন্ রণাঙ্গনে যেতে হবে আমাকে?
রণাঙ্গন? না না যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হবে না তোমাকে আদৌ! তোমার কাজ এই ওয়াশিংটনেই!
বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ে গ্রোভস। নীরবে তার বদলির অর্ডারখানা বাড়িয়ে ধরে। সেটা ‘ওভারসিজ অ্যাসাইনমেন্ট’–সাগরপারে যাবার নির্দেশবহ।
-হ্যাঁ, হ্যাঁ জানি। আমরা চেয়েছিলাম, তোমার সহকর্মীরা ভুল খবরই পাক। মানে, তুমি যেন বিদেশ যাচ্ছ। আসলে তোমাকে আমরা নিয়োগ করছি মানহাটান প্রকল্পের সর্বময় কর্তারূপে। কাজটা তোমার মতো এঞ্জিনিয়ার-যোদ্ধার উপযুক্ত।
ধরা গলায় গ্রোভস বলে, জেনারেল। আমি কোনো এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করিনি। এই ‘এঞ্জিনিয়ার যোদ্ধার’ খেতাব থেকে এবার আমি মুক্তি পেতে চাই। আপনি দয়া করে
জেনারেল ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলেন, কর্নেল, যে কাজটা তোমাকে দেওয়া হচ্ছে সেটা এ বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আইসেনহাওয়ার, প্যাটন অথবা মন্টির ওপর যতটা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার চেয়ে একচুলও কম নয়। দ্বিতীয়ত, এজন্য তোমাকে নির্বাচন করেছেন যুদ্ধসচিব হেনরি স্টিমসন নিজে–অন্তত দশজন সম্ভাব্য ক্যান্ডিডেটের ভিতর থেকে বেছে নিয়ে। শেষ কথা, প্রেসিডেন্ট স্বয়ং তোমার নিয়োগপত্রে সই দিয়েছেন। কিছু বলবে?
বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইল লেসলি গ্রোভস।
***
মানহাটান প্রকল্পের সর্বময় কর্তৃত্ব নিয়ে ঘূর্ণিঝড়ের মতো সব কয়টি কেন্দ্র একবার করে ঘুরে এল গ্রোভস। সব কয়টি কেন্দ্র সরেজমিনে দেখল। প্রতিটি কেন্দ্রের উচ্চপদস্থ বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে আলাপ হল, পরিচয় হল। অবাক হয়ে গেল সে।
সর্বপ্রথমেই সে এল নিউইয়র্কে, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা কাঁটাতারে ঘেরা অংশ। এখানে নাকি গ্যাসীয়-ডিফিউশন পদ্ধতিতে ইউরেনিয়ামকে পৃথককরণ করার প্রচেষ্টা হচ্ছে। ইউরেনিয়াম-ওর’ থেকে ইউ-235 নিষ্কাশনের প্রচেষ্টা। বাইরে সাইনবোর্ড টাঙানো আছে, ‘এস. এ. এম.’ অর্থাৎ Substitute Alloy Materials। লোকচক্ষুকে বিভ্রান্ত করার জন্যই এ অদ্ভুত নাম। ল্যাবরেটারির কর্ণধার ডক্টর হারল্ড ইউরে(1893-1981)–নোবেল লরিয়েট রসায়নবিজ্ঞানী। কিন্তু দৈনিক কাজকর্ম দেখাশোনা করেন ড. ড্যানিং, পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের উৎসাহী বৈজ্ঞানিক। ওঁরা দুজনে গ্রোকে নিয়ে গ্যাসীয় ডিফিউশন পদ্ধতি দেখাবার জন্য বার হলেন। কিন্তু গ্রোভস বাধা দিয়ে বললে, ডক্টর ইউরে, ল্যাবরেটারি পরিদর্শনের আগে দয়া করে আমাকে বুঝিয়ে দিন গ্যাসীয় ডিফিউশন পদ্ধতিটাই বা কী, আর কেন ওটা করতে চাইছেন।
ডক্টর ইউরে বলেন, তার আগে আপনি বলুন–পারমাণবিক-বোমা জিনিসটা কীভাবে বাস্তবায়িত হতে পারে সেটা কি আপনি বুঝেছেন? জানেন?
-ভালোভাবে নয়। মূল তত্ত্বটা আমাকে দয়া করে বলুন।
ডক্টর ইউরে যা বললেন তার সংক্ষিপ্তসার এইরকম—
ইটালিতে ফের্মি এবং জার্মানিতে অটো হান ইতিপূর্বেই ইউরেনিয়াম পরমাণুর অন্তর বিদীর্ণ করেছেন। তাতে ইউরেনিয়াম পরমাণু দু-টুকরো হয়ে রূপান্তরিত হয়েছে ক্রিপটন আর বেরিয়ামে। পারমাণবিক শক্তিও জন্ম নিয়েছে–কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য। তা হোক, ওই সঙ্গে আমরা দেখেছি নূতন দু-তিনটি নিউট্রন বিমুক্ত হয়েছে। সেই দু-তিনটি নিউট্রন তীব্রবেগে ছুটে গেছে এবং অন্যান্য পরমাণুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে শেষ পর্যন্ত থেমে গেছে। এখন যদি এমন ব্যবস্থা করা যায় যে, ওই দু-তিনটি নবলব্ধ নিউট্রন আর দু-একটি পরমাণুর অন্তর বিদীর্ণ করবে তবে আমরা আবার কিছু শক্তি পাব এবং পাব দুই-দুগুণে চারটে নতুন নিউট্রন। সে দুটি আবার চার-দুগুণে আটটা, তা থেকে আট-দুগুণে ষোলোটা নিউট্রন মুক্ত হতে পারে। এইভাবে বিশ-ধাপ চললেই লক্ষ লক্ষ নিউট্রন মুক্ত হবে, পঁচিশ ধাপে কোটি কোটি পরমাণু বিদীর্ণ হয়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটাবে! ব্যাপারটার চিত্রকল্প হবে এই রকম (চিত্র 7)। লক্ষণীয়, চিত্র 6-তে আমরা দেখিয়েছি, ইউরেনিয়াম পরমাণু বিদীর্ণ হওয়ায় তিনটি নিউট্রন ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল। চিত্র 7-এ তার যে-কোনো দুটির চেন-রিয়্যাকশন দেখানো হয়েছে। তিনটিই যদি কার্যকরী হয় তাহলে অঙ্কশাস্ত্র মতে 3-9-27-81….এভাবেও চেন রিয়্যাকশন হতে পারে।]
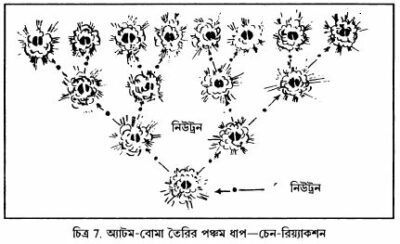
[চিত্র 7. অ্যাটম-বোমা তৈরির পঞ্চম ধাপ—চেন-রিয়্যাকশন]
মজা হচ্ছে এই যে, এটা তখনই সম্ভব যখন মুক্ত নিউট্রনের আশেপাশে যথেষ্ট পরিমাণ ইউ-235 পরমাণু থাকবে। দুর্ভাগ্যক্রমে আকরিক ইউরেনিয়ামে প্রতিটি ইউ-235-এর জায়গায় দেড়শটি ইউ-238 থাকে। ফলে অধিকাংশ নিউট্রনই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। চিত্র 8-এ ব্যাপারটা বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে। কালো কালো বলগুলি ইউ-235 সাদাগুলি ইউ-238। বাঁ-দিক থেকে আমরা তিনটি নিউট্রন বুলেট ছেড়েছি। ধরা যাক দু-নম্বর বুলেট ঘটনাস্থলে গিয়ে একটি ইউ-235 চিত্র 8. নিউট্রন-বুলেট পরমাণুকে বিদ্ধও করল, তা থেকে দুটি নূতন নিউট্রনও বিমুক্ত হল। কিন্তু চেন-রিয়্যাকশান হওয়ার সম্ভাবনা কোথায়? চতুর্দিকেই যে ইউ-238।
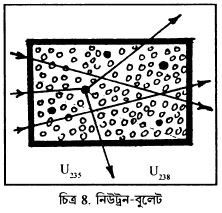
[চিত্র 8. নিউট্রন-বুলেট]
ইউরে বললেন, সেজন্য আমরা এখানে আকরিক ইউরেনিয়াম থেকে ইউ-235–কে পৃথককরণ করছি। এমন অবস্থা করতে চাই যাতে নিউট্রন-বুলেটকে যে ভীড়ের দিকে ছোঁড়া হবে সেখানে শুধুমাত্র ইউ-235ই থাকবে। তাহলে চিত্র 7-এর মতো চেন-রিয়্যাকশান, অর্থাৎ চক্রবর্তন-পদ্ধতি, চালু হয়ে যাবে–দুই, চার, আট, ষোললা, বত্রিশ, চৌষট্টি ইত্যাদি-ইত্যাদি। অর্থাৎ পঁচিশ-তিরিশ ধাপ পরে কোটি কোটি পরমাণুর বিস্ফোরণ।
কীভাবে সেটা করতে চান?
–ইউরেনিয়াম থেকে উৎপন্ন ইউরেনিয়াম হেক্সাফ্লুরাইড গ্যাসকে উত্তপ্ত করে একটা ফিলটার টিউব-এর ভেতর দিয়ে পাঠাতে হবে। ওই ফিলটার টিউবে থাকবে অসংখ্য অতিক্ষুদ্র ছিদ্র। তাহলে হালকা ইউ-235 পরমাণুগুলো ভারী ইউ-238 পরমাণু থেকে পৃথক হয়ে যাবে।
-বুঝলাম।
-আজ্ঞে না, বোঝেননি। প্রথমত ইউরেনিয়াম হচ্ছে সবচেয়ে ভারী ধাতু। তাকে তরল এবং শেষমেশ গ্যাসে রূপান্তরিত করাই এক ঝকমারি ব্যাপার। প্রচণ্ড উত্তাপ লাগে। দ্বিতীয়ত, গ্যাসীয় ইউরেনিয়াম অত্যন্ত করোসিভ; পাইপগুলো ক্ষয়ে যাচ্ছে। তৃতীয়ত, ওই যে আমি বললাম, ‘অসংখ্য ছোটো ছোটো ছিদ্র’ ওটা তো অবৈজ্ঞানিক উক্তি। অসংখ্য’ শব্দটার অর্থ হচ্ছে কয়েক শত কোটি! এবং ছোটো ছোটো’ শব্দটার ব্যাখ্যা হচ্ছে প্রতিটি ছিদ্রের ব্যাস এক মিলিমিটারের দশ হাজার ভাগের একভাগ!
গ্রোভস, রুমাল দিয়ে মুখটা মুছলেন।
–আমার বক্তব্যটা শেষ হয়নি জেনারেল। ইউরেনিয়াম 238 অত্যন্ত দুর্লভ ও দুর্মূল্য পদার্থ। আর তা থেকে আমরা পরমাণু বোমা বানানোর উপযুক্ত ইউরেনিয়াম 235 পাচ্ছি 0.7 শতাংশ। অর্থাৎ প্রায় দেড়শ গ্রামে এক গ্রাম।
গ্রোভস ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় হলেন।
***
পরবর্তী পরিদর্শন শিকাগোতে। এখানে ইউরেনিয়াম নয়, প্লুটোনিয়াম নিয়ে পরীক্ষা হচ্ছে। সর্বময় কর্তা আর্থার কম্পটন (1892-1962)। তিনি ছাড়া আরও দুজন নোবেল-লরিয়েট করমর্দন করলেন গ্রোদ্রে সঙ্গে। তারা হচ্ছেন ইটালিয়ন ফের্মি এবং জার্মান ফ্রাঙ্ক। দুজনেই ফ্যাসিস্ট আর নাৎসি রাজ্যের প্রাক্তন বাসিন্দা। ফের্মি এসেছেন পালিয়ে, ফ্রাঙ্ক বিতাড়িত হয়ে। গোটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এছাড়াও ওঁর সঙ্গে মিলিত হলেন উইগনার আর ৎজিলাৰ্ড–যাঁরা গিয়েছিলেন আইনস্টাইনের পত্র আহরণে।
এর ভিতর ইউজিন উইগনার (1902-1995) একটি অদ্ভুত চরিত্র। এঁর কথা আগে বিস্তারিত বলা হয়নি। এই প্রতিভাশালী হাঙ্গেরীয় পদার্থবিজ্ঞানীর সৌজন্য আর ভদ্রতা-জ্ঞান ছিল প্রবাদের মতো। মেজাজ খারাপ করা জিনিসটা যে কী, তা তিনি জানতেনই না। ৎজিলাৰ্ড তার স্মৃতিচারণে লিখেছেন, উইগনারের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে দীর্ঘদিন মিশেছি। এমন অমায়িক ভদ্র মানুষ আর হয় না। কখনও তাকে রাগতে দেখিনি, কখনও কাউকে গালাগাল করতে শুনিনি। না! ভুল বললাম। জীবনে একবার তাকে রাগতে দেখেছিলাম। সেবারে উনি আমাকে গাড়ি করে কোথায় যেন নিয়ে যাচ্ছিলেন। উনি বসেছেন স্টিয়ারিঙে, আমি ওঁর পাশে। কোথাও কিছু নেই ‘ট্রাফিক-রুলস’ শিকেয় তুলে ওপাশ থেকে একটা গাড়ি হুড়মুড় করে এসে পড়ল আমাদের সামনে। উইগনার কোনক্রমে ব্রেক কষে দুর্ঘটনা এড়িয়ে ফেলেন। দুটো গাড়িই দাঁড়িয়ে পড়েছে। লক্ষ্য করে দেখি, ওপাশের গাড়িটার চালক মদে চুর হয়ে আছে। সেই একদিন উইগনারকে ক্ষেপে যেতে দেখেছিলাম। হঠাৎ চীৎকার করে উইগনার বললেন : “গো টু হেল–” পরমুহূর্তেই স্বভাববিনয়ী স্বতঃস্ফূর্তভাবেই ছোট্ট করে যোগ করলেন “প্লিজ!”
শিকাগো গ্রুপের কর্তা ছিলেন কম্পটন; কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র হচ্ছেন এনরিকো ফের্মি। উনি কম কথার মানুষ। সব আলোচনাতেই দেখা যেত তিনি তার অভিমত জানাতেন সবার শেষে। আর অনিবার্যভাবে প্রমাণ হত–ফের্মির বক্তব্যই নির্ভুল। অথচ অত্যন্ত নিরভিমানী ব্যক্তি। আত্মপ্রশংসা যে তিনি করতেন না তা নয় কিন্তু তার ক্ষেত্র বিজ্ঞান নয়। নিজে যে একজন মস্ত সাঁতারু, মস্ত পর্বতারোহী অথবা গোয়েন্দা গল্পের আসল অপরাধীকে সবার আগে ধরে ফেলার পারদর্শিতা তার আছে একথা সাড়ম্বরে বলতেন। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ উঠলেই উনি সঙ্কুচিত হয়ে পড়তেন। বলতেন–এত সব জ্ঞানীগুণীরা আছেন, ওঁদের জিজ্ঞাসা করুন। ফের্মির একটি বিলাস ছিল কম্পুটারের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া। ওঁর ছোট্ট স্লাইড-রুল হাতে উনি কম্পুটারের সঙ্গে লড়াই করতেন। কখনও উনি জিততেন, কখনও কম্পুটার। মানসাঙ্কে এমনই অদ্ভুত প্রতিভা ছিল তার।
ফ্রাঙ্কের কথা আগেই বলেছি। সহকর্মীদের অপমানে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে দেশত্যাগী হয়েছিলেন ফ্রাঙ্ক। আভিজাত্য ছিল তার রক্তে।
বাকি রইল শিকাগো-গ্রুপের কর্তা আর্থার কম্পটনের পরিচয়। ওঁর সহকর্মীরা ঠাট্টা করে বলত, কম্পটন শিকাগো-গ্রুপের প্রকৃত লিডার নন,-ডেপুটি লিডার। মূল নিয়ামক হচ্ছেন তার গিন্নিবেটি কম্পটন। নোবেল-লরিয়েট প্রৌঢ় কম্পটন হাসতেন সেকথা শুনে। কারণ ছিল! তাকে যখন শিকাগো-গ্রুপের কর্তৃত্ব দেবার প্রস্তাব হল কম্পটন সরাসরি বড়কর্তাদের বলেছিলেন, আমি এক শর্তে এ পদ গ্রহণ করতে রাজি আছি।
-কী শর্ত বলুন?
–আমার স্ত্রীকেও ক্লিয়ারেন্স দিতে হবে। পদাধিকারবলে আমি যেসব গুপ্ত কথা জানব তা আমার স্ত্রীকেও জানাতে পারি আমি। পদাধিকারবলে আমি যেসব গোপন স্থানে যাব, আমার স্ত্রীরও সেখানে যাবার অধিকার থাকবে।
এ অদ্ভূত অনুরোধে অবাক হয়েছিলেন কর্তৃপক্ষ। তবু মেনে নিয়েছিলেন তারা। বেটি কম্পটন শিকাগো ল্যাবরেটারির নানান কাজ করতেন। সবাই তার আদেশ মেনে চলত। সর্বজনশ্রদ্ধেয়া কর্ত্রীই ছিলেন তিনি শিকাগো বীক্ষণাগারে।
***
গ্রোভস পরিদর্শনে আসায় ওঁরা তাঁকে নিয়ে বসালেন লেকচার হলে। গ্রোভস প্রশ্ন করলেন, একটা পরমাণু বোমার জন্য কতটা প্লুটোনিয়াম দরকার?
ফ্রাঙ্ক বললেন, সেটা নির্ভর করছে আপনি কত বড় বোমা চান তার ওপর।
–ধরুন দশ হাজার টন TNT-বোমার বিস্ফোরণের উপযুক্ত পারমাণবিক বোমা।
তৎক্ষণাৎ শুরু হয়ে গেল যোগ-বিয়োগ-ইনটিগ্র্যাল ক্যালকুলাসের অঙ্ক। ব্ল্যাকবোর্ডে পড়তে শুরু করল হিজিবিজি লেখা। হাতির শুড়ের মতো চিহ্ন সব। আলফা-বিটা-থিটা-এপসাইলনের বন্যায় ভেসে গেলো কালো বোর্ড। সবাই তাকিয়ে আছে একদৃষ্টে ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে। একমাত্র ব্যতিক্রম এনরিকো ফের্মি। তিনি আপন মনে স্লাইড রুল ঘষছেন। হঠাৎ গ্রোভস-এর নজর হল পঞ্চম ধাপ থেকে ষষ্ঠ ধাপে আসবার সময় একটা ভুল হয়েছে। বুঝতে পারলেন না ব্যাপারটা। তিন-তিনজন নোবেল-লরিয়েট বিজ্ঞানী উপস্থিত রয়েছেন! আছেন ৎজিলাৰ্ড, উইগনারের মতো বিচক্ষণ বিজ্ঞানী। ওঁর মনে হল এটা কি ওঁরা ইচ্ছা করে কাঁদ। পেতেছেন? মানহাটান প্রকল্পের সর্বময় কর্তা কতটা অঙ্ক বোঝেন তাই কি বুঝে নিতে চান তারা। তা সে যাই হোক, হঠাৎ উঠে দাঁড়ান তিনি। বলেন, মাপ করবেন, ওই ষষ্ঠ ধাপটা আমি বুঝতে পারছি না। ওর আগের ধাপের 10^5 পরের ধাপে হঠাৎ 10^6 হল কেমন করে?
গণিতজ্ঞ তৎক্ষণাৎ বলেন, ধন্যবাদ। ওটা নিছক ভুলই।
ভুলটা সংশোধন করেন তিনি। গ্রোভস আত্মবিশ্বাস ফিরে পান।
শেষ ফলাফলটা যখন বলা হয় তখন গ্রোভস জানতে চাইলেন–আপনাদের এই সংখ্যা কত পার্সেন্ট শুদ্ধ? অর্থাৎ কতটা এদিক-ওদিক হতে পারে?
কম্পটন তৎক্ষণাৎ বলেন, ধরুন দশ পার্সেন্ট শুদ্ধ!
এমন আজব কথা জীবনে শোনেনি গ্রোভ! বললেন মাত্র দশ পার্সেন্ট! বলেন কি?
-হ্যাঁ। বর্তমানে এর চেয়ে নির্ভুল উত্তর অঙ্কশাস্ত্র মতে আর পাওয়া যাচ্ছে না।
গ্রোভস তখন ভাবছিলেন একটা নিমন্ত্রণ বাড়ির কথা। ক্যাটারারকে উনি বলছেন, আজ আমার বাড়ি কিছু লোক খাবে। খাবারের যোগাড় দিতে হবে আপনাকে। দেখবেন, খাবারে কম না পড়ে যেন। আর অপচয়ও না হয়।
ক্যাটারার জানতে চাইল, কতজন লোক খাবে স্যার?
–এই ধরুন জনা দশেক অথবা হাজারখানেক!
শতকরা দশভাগ নির্ভুল উত্তর। কারণ ‘দশ’ হচ্ছে একশর দশ-শতাংশ। নির্ভুল উত্তর, আবার ‘হাজার’-এর দশ-শতাংশ। নির্ভুল উত্তর হচ্ছে ‘একশ’! করো এবার আহারের আয়োজন!
***
শিকাগো ল্যাবরেটারি পরিদর্শন সেরে ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল গ্রোভসস আসছিলেন ফ্রাঙ্কের অ্যাপার্টমেন্টে। সেখানেই তার নৈশ-আহারের ব্যবস্থা। ফ্রাঙ্ক নৈশাহারে নিমন্ত্রণ করেছেন পরিদর্শককে। শহরের অপর প্রান্তে একটা নয়তলা বাড়ির একটি অ্যাপার্টমেন্টে তখন বাস করতেন সস্ত্রীক জে ফ্রাঙ্ক। গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ফ্রাঙ্ক নিজে, পাশে বসে আছেন গ্রোভস। কথাপ্রসঙ্গে ফ্রাঙ্ক বললেন, আমি বুঝতে পারছি আপনার অবস্থাটা! টেন পার্সেন্ট কারেক্ট উত্তর দিয়ে আপনি কী করবেন? কতটা প্লুটোনিয়াম লাগবে, কতটা ফিশনের মেটিরিয়াল লাগবে কিছুই বুঝতে পারছেন না। কিন্তু কী করা যাবে বলুন? আর কিছুদিন গবেষণা না করলে আমরা ওর চেয়ে কিছু কম-ভুল ফিগার দিতে পারছি না।
গ্রোভস সহানুভূতি দেখিয়ে বলেন, বুঝেছি। তবু হতাশ হবার কিছু নেই। আপনাদের সামনে কী পরিমাণ বাধা তা বুঝতে পারছি আমি।
ফ্রাঙ্ক হেসে বলেন, না! পারছেন না। আমার সাফল্যের সামনে সবচেয়ে বড় বাধা কী জানেন?
–কী?
–ফ্রাউ ফ্রাঙ্ক।
অবাক হয়ে যান গ্রোভস। কী বলবেন ভেবে পান না। দাম্পত্য জীবনে ফ্রাঙ্ক কি অসুখী? তবু সে কথা এমন সদ্যপরিচিত লোকের কাছেই বা উনি বলবেন কেন? ফ্রাঙ্ক অভিজাত পরিবারের মানুষ, আত্মমর্যাদাজ্ঞান তার প্রখর। এমন বেমক্কা একটা পারিবারিক রহস্য কেন উঘাটিত করে বসলেন তিনি?
ডিনার টেবিলে সৌজন্য বজায় রেখে মামুলি প্রশ্ন করেন গ্রোভস। শ্রীযুক্তা ফ্রাঙ্ক অতি অমায়িক মহিলা। দেখলে বোঝা যায়, এককালে খুবই সুন্দরী ছিলেন। মার্জিত, অভিজাত এবং সদাহাস্যময়ী আদর্শ হোস্টেস। অতিথির আপ্যায়নে কোনো ত্রুটি থাকল না। আলাপ হল নানা বিষয়ে পানাহারের ফাঁকে ফাঁকে। ফ্রাই ফ্রাঙ্ক তার ছেলেবেলায় গল্প শোনালেন। ব্যাভেরিয়ায় তার বাড়ি। ব্যাভেরিয়ার রাজপ্রাসাদে, সেখানকার চিত্রশালা, বিয়ার-পার্ক, চার্চ–কত স্মৃতিকথা। মার্কিন জীবনযাত্রার সঙ্গে জার্মান জীবনের তুলনা করলেন। ওঁদের জার্মানি থেকে চলে আসার প্রসঙ্গ উঠল। হিটলারের ইহুদি নির্যাতনের প্রতিবাদে প্রফেসর ফ্রাঙ্ক পদত্যাগ করে। দেশত্যাগী হলেন। কোনো সভাসমিতির আয়োজন নিষিদ্ধ ছিল। ওঁর এক জার্মান সহকারী এবং শিষ্য ক্যারিও খবর পেয়ে গোপনে দেখা করতে এল। অধ্যাপকের হাতে তুলে দিল একটা প্রকাণ্ড অ্যালবাম। ফটোগ্রাফির সখ ছিল ক্যারিওর। গোটিনজেন-এর অসংখ্য ছবি তুলেছে সে। সাজিয়েছিল ওই অ্যালবামে। প্রফেসর ফ্রাঙ্ক ইতস্তত করে বলেছিলেন, তোমার এত সাধের সংকলনটা আমাকে দিয়ে দেবে? অরুদ্ধ কণ্ঠে ক্যারিও বলেছিল, প্রফেসর, আমি যে খাঁটি আর্য! গোটা গোটিনজেনটাই তো রইল আমার ভাগ। তার ছায়াটুকুই তো শুধু আপনাকে দিচ্ছি।
গ্রোভস্ কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করেন, অ্যালবামটা নিয়ে এসেছেন তো এখানে?
ফ্রাই ফ্রাঙ্ক উঁকি মেরে দেখলেন, প্রফেসর ফ্রাঙ্ক প্যান্ট্রিতে কয়েকপাত্র মার্টিনি বানাতে ব্যস্ত। চুপি চুপি বলেন, প্রফেসর অবসর পেলেই সেটার পাতা ওল্টান। ওই অ্যালবামটাই ওঁর প্রাণ। উনি গোটিনজেনকে যতটা ভালোবেসেছিলেন ততটা আমাকেও বাসেননি। গোটিনজেন ছিল আমার সতীন।
দুজনেই হেসে ওঠেন।
শ্ৰীমতী ফ্রাঙ্ক বলেন, অথচ মজা কী জানেন জেনারেল? প্রফেসর এই অ্যালবামটা নিয়ে এলেন তার পোর্টম্যান্টোতে–রেখে এলেন নোবেল প্রাইজের সোনার মেডেলটা!
-সে কী! ওটার আর কতটুকু ওজন?
-না, ওজনের জন্য নয়। ওঁর যুক্তি অন্য রকম। বললেন, মেডেলটা তো একা জেমস ফ্রাঙ্ক পায়নি–পেয়েছে গোটা বিশ্ববিদ্যালয়! ওটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটারিতেই থাকবে। ল্যাবরেটারিতেই রেখে এসেছেন সেটাকে!
গ্রোভস্ চমকে ওঠেন। বলেন, সর্বনাশ! গেস্টাপো সেটা খুঁজে পেলে গলিয়ে ফেলবে! সোনাটা ওয়্যার-ফান্ডে জমা দেবে!
ততক্ষণে ফিরে এসেছেন প্রফেসর ফ্রাঙ্ক কয়েকপাত্র পানীয় ট্রেতে করে নিয়ে। বলেন, আপনি ব্যস্ত হবেন না জেনারেল। ওরা সেটা খুঁজে পাবে না।
-মাটির নীচে পুঁতে রেখে এসেছেন?
–না। কারণ তাহলে ওরা খুঁজে পেত। আমি সেটা ফেলে রেখে এসেছি একটা নাইট্রিক অ্যাসিডের বোতলে! যুদ্ধের পরে ঠিক সেটা খুঁজে পাওয়া যাবে, দেখবেন আপনি।* [* প্রফেসর ফ্রাঙ্কের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছিল। ফ্রাঙ্কই একমাত্র নোবেল-লরিয়েট যিনি এক নোবেল প্রাইজ দুবার পেয়েছেন। যুদ্ধান্তে নাইট্রিক-অ্যাসিডের বোতলের তলদেশ থেকে যখন সোনার মেডেলটি উদ্ধার করা গেলো তখন দেখা গেল তার লেখা কিছু কিছু ক্ষয়ে গেছে। খবরটা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। তাতে সুইডেনের আকাঁদেমি ফ্রাঙ্কের কাছ থেকে মেডেলটি ফেরত নেয়-নূতন করে ছাপ দিয়ে পরের বছর উৎসবের সময় সেই মেডেলটি ফ্রাঙ্ককে দ্বিতীয়বার উপহার দেওয়া হয়।]
গ্রোভস বলেন, সে যাই হোক, আপনি জার্মানি থেকে বিদায়পর্বের গল্প বলেছিলেন–
শ্ৰীমতী ফ্রাঙ্ক তার গল্পের সূত্র তুলে নেন–
ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিল কয়েকজন। অনাড়ম্বর বিদায়পর্ব। গোটিনজেন-এর মধ্যমণি চিরদিনের মতো বিদায় নিচ্ছেন। তাকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছেন মাত্র জনা-পাঁচেক সহকর্মী ও ছাত্র। প্রফেসর হিলবার্ট, হেইসেনবের্গ, ক্যারিও প্রভৃতি। ফ্রাঙ্ক সস্ত্রীক গাড়িতে উঠে বসলেন। গার্ড হুইসিল দিল। সবুজ পতাকা নাড়াল। কিন্তু কী-এক যান্ত্রিক গণ্ডগোলে ইঞ্জিনটা চালু হল না। ঠিক সেই মুহূর্তেই স্টেশনের একজন কুলি এমন একটা কথা বলে বসল যা ফ্রাই ফ্রাঙ্ক জীবনে ভুলবেন না। লোকটি এগিয়ে এসে অধ্যাপক ফ্রাঙ্ককে বললে, হের প্রফেসর! একটা জিনিস খেয়াল করেছেন? হিটলারের ওই মাথামোটা অফিসারগুলো যে সহজ হিসাবটা বুঝল না, সেটা ওই জড় ইঞ্জিনটাও বুঝে ফেলেছে! সে প্রতিবাদ জানাচ্ছে! আপনাকে নিয়ে যেতে সে রাজি নয়!
গল্পগুজবে কথাবার্তায় প্রায় মধ্যরাত্রি হয়ে গেল। গ্রোভস মনে মনে ভাবছিলেন অন্য একটি কথা। অধ্যাপক কেন তখন বললেন–তাঁর সাফল্যের পথে প্রধান বাধা হচ্ছেন ফ্রাই ফ্রাঙ্ক। এমন অমায়িক সুন্দরী সপ্রতিভ স্ত্রীর বিরুদ্ধে কী তার অভিযোগ? বুঝে উঠতে পারলেন না সেটা। যাই হোক, মধ্যরাত্রে গ্রোভস্ বিদায় নিয়ে উঠে পড়েন। ওঁরা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন অতিথিকে গাড়িতে তুলে দিতে। বিদায় বেলায় গ্রোভস্ গৃহস্বামীকে বললেন, আপনাদের আতিথেয়তার কথা জীবনে ভুলব না আমি!
কোথাও কিছু নেই ধক্ করে জ্বলে উঠল শ্রীযুক্তা ফ্রাঙ্কের নীল চোখ দুটো। যেন অপমানকর কোনো উক্তি করেছেন গ্রোভস। মুহূর্তে বদলে গেলেন তিনি। বললেন, কী বললেন? কোনোদিন ভুলবেন না? কোনো দিন নয়?
গ্রোভস স্তম্ভিত! কী হল হঠাৎ! এমন বদলে গেলেন কেন উনি?
অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে বললেন, প্লিজ ডার্লিং! জেনারেল আমাদের অতিথি!
ঘুরে দাঁড়ালেন মহিলা। স্বামীর মুখোমুখি। দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, সো হোয়াট? অতিথি-সৎকার তো আমি চুটিয়ে করেছি জেম। ত্রুটি রাখিনি কিছু। এবার আমাকে ব্যাপারটা সমঝিয়ে নিতে দাও।
হতাশ হয়ে শ্রাগ করলেন অধ্যাপক।
গৃহস্বামিনী আবার ঘুরে দাঁড়ালেন গ্রোভস-এর দিকে। মুখোমুখি। অসমাপ্ত বাক্যটার জের টেনে পুনরায় বলেন, কী বলছিলেন? কোনো দিন ভুলবেন না? আমার শ্বশুরবাড়ি হ্যান্সবুর্গ অথবা আমার বাপের বাড়ি ব্যাভেরিয়ায় যেদিন ওই অ্যাটম-বোমটি নিক্ষেপ করার আদেশ জারি করবেন সেদিনও নয়? আমার স্বামী সাফল্যমণ্ডিত হওয়া মাত্রই তো সে আদেশ জারি করবেন আপনি, হের জেনারেল। তাই নয়?
গ্রোভস-এর মাথা নীচু হয়ে গেল। মাটিতে একেবারে মিশে যেতে ইচ্ছে হল তার। ভুল। মারাত্মক ভ্রান্তি। এতক্ষণ ওঁর খেয়াল হয়নি–ওঁরা দুজন জার্মান। জার্মানিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করার ব্রত নিয়েই তিনি আজ মানহাটান প্রকল্পের সর্বময় কর্তা। নোবেল-লরিয়েট জেমস্ ফ্রাঙ্ক মাতৃভূমিকে শ্মশানে রূপান্তরিত করবার সংকল্প নিয়েই প্রাণপাত করছেন। তাই তার সাফল্যের পথে আজ সবচেয়ে বড় বাধা–ফ্রাই ফ্রাঙ্ক!
হে ঈশ্বর! প্রথম পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণ যেন অন্তত ওই ব্যাভেরিয়াতে না হয়!
.
০৭.
তৃতীয় পরিদর্শন যুক্তরাষ্ট্রের একেবারে পশ্চিমপ্রান্তে। বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ে। এখানকার সর্বময় কর্তা ই. ও. লরেন্স (1901-1958)। তিনিও নোবেল-লরিয়েট (1939)। দীর্ঘদেহী, প্ল্যাটিনাম-ব্লন্ড চুল, অথচ মুখখানা ছেলেমানুষের মতো অপাপবিদ্ধ। প্রফেসর লরেন্স গাড়ি নিয়ে নিজেই এসেছিলেন সানফ্রান্সিস্কো এয়ারোড্রামে। গ্রোভস আত্মপরিচয় দিতে সহৃদয় করমর্দন করে বললেন, জেনারেল, আমি শুনেছি ইতিমধ্যে আপনি কলোম্বিয়া আর শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় ঘুরে এসেছেন। এখানে আমরা অনেকটা এগিয়ে আছি। চলুন, আমরা সরাসরি রেডিয়েশান হিল-এ যাব–মানে আমাদের ল্যাবরেটারিতে।
দীর্ঘ পথশ্রমে গ্রোভস্ ছিলেন ক্লান্ত। কিন্তু তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলেন তিনি। শিকাগো এবং নিউ ইয়র্কের অবস্থা দেখে হতাশ হয়েছেন–এখানে লরেন্স বলছেন, কাজ অনেকটা এগিয়ে আছে। বেশ, দেখাই যাক।
লরেন্স নিজেই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেলেন ওঁকে। গ্রোভস তার যুদ্ধ পরবর্তী স্মৃতিচারণে বলেছেন, “যুদ্ধ চলাকালে আমার জীবনে সবচেয়ে লোমহর্ষক কটি মুহূর্ত ছিল সানফ্রান্সিস্কো থেকে রেডিয়েশান হিল-এ আসা। মনে হল, আমি বুঝি মোটর রেসিং-এর প্রতিযোগী। নক্ষত্ৰবেগে গাড়ি চালালেন লরেন্স, কোনো ট্রাফিক-রু না মেনে। স্থানীয় লোকেরা বোধহয় গাড়িটাকে চেনে, পুলিস-পুঙ্গবেরাও এই পাগলা নোবেল-লরিয়েট ড্রাইভারের গাড়ির নম্বর-প্লেটের সঙ্গে পরিচিত। না হলে এই দশ মিনিট ড্রাইভিং-এ দশটা নোটবুকে ওঁর গাড়ির নম্বর উঠে যাবার কথা।
“ঈশ্বরকে ধন্যবাদ–আমরা আধঘণ্টার পথ দশমিনিটে পাড়ি দিয়ে অক্ষত শরীরে এসে উপস্থিত হলাম গন্তব্যস্থলে। প্রফেসর লরেন্স সুইচ-অফ করে বলেন, আসুন।
“আমি বলি, একটু অপেক্ষা করুন প্রফেসর। নোটবইতে একটা কথা লিখে রাখি।
“গাড়ি থেকে নামবার আগেই নোটবইতে লিখে রাখলাম–আর্নেস্ট লরেন্স-এর গাড়ির জন্য একটি সরকারি ড্রাইভার নিযুক্ত করতে হবে। লরেন্সকে স্টিয়ারিঙে বসতে দেওয়া হবে না। হেড-কোয়াটার্সে পোঁছে এটাই হবে আমার প্রথম ডিটেশান। সামরিক আদেশ।”
লরেন্স ওঁকে বিচিত্রদর্শন একটি যন্ত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এটা তার নিজস্ব আবিষ্কার। সদ্য আবিষ্কৃত। নাম হচ্ছে ক্যালুট্রন। ক্যালু” হচ্ছে। ক্যালিফোর্নিয়ার স্মৃতিবাহী, আর “ট্রন” সাইক্লোট্রন যন্ত্রের শেষাংশ। গ্রোভস সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেন, এতে কী হয়?
এক গাল হাসলেন লরেন্স। সে হাসিতেই যেন জবাব-অপুত্রের পুত্র হয়, নির্ধনের ধন! ইহলোকে সুখি, অন্তে গোলোকে গমন!
-বলছি শুনুন। আপনি জানেন–আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইউ-238 থেকে ইউ-235কে বিচ্ছিন্ন করা। কলোম্বিয়াতে ওঁরা সেটা করতে চাইছেন ছ্যাঁদাওয়ালা টিউবের মধ্য দিয়ে গ্যাসীয় অবস্থায় ইউরেনিয়ামকে পাঠিয়ে। আমার এটা হচ্ছে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পদ্ধতি। এই ক্যালুট্রন যন্ত্রে আছে একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী ম্যাগনেটিক ফিল্ড। গ্যাসীয় অবস্থায় ইউরেনিয়াম যখন এই যন্ত্রের মধ্য দিয়ে যাবে তখন চৌম্বক-আকর্ষণে হালকা ইউ-235 অপেক্ষাকৃত ভারী ইউ-238 থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। ব্যাপারটা কেমন জানেন? মনে করুন একই ফোর্সে দুটি পাথরকে ছোঁড়া হল–একটা ভারী একটা হালকা। তাহলে কী হবে? হালকা পাথরটা এগিয়ে যাবে, নয় কি?
সহজ ব্যাখ্যা। গ্রোভস্ প্রশ্ন করেন, কতক্ষণ চালানো হবে যন্ত্রটা?
–অন্তত চব্বিশ ঘন্টা।
–চালিয়ে দেখেছেন? কত পার্সেন্ট সেপারেশন হচ্ছে?
–না জেনারেল। যন্ত্রটা মিনিট পনেরোর বেশি চালানো যাচ্ছে না বর্তমানে। যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিচ্ছে তার মধ্যে। গরম হয়ে যাচ্ছে।
-বলেন কী? তাহলে এতদিনে কতটুকু ইউ-235 পেয়েছেন?
-না, না, এখনও আমরা একটুও ইউ-235 পাইনি। তবে পাব, শীঘ্রই পাব। কী বলেন?
***
সব কয়টি কেন্দ্র ঘুরে গ্রোভস্ এসে দেখা করলেন যুদ্ধসচিবের সঙ্গে।
বললেন, স্যার, একজন বৈজ্ঞানিক সহকারী আমার চাই। পদার্থবিজ্ঞানী। বে-সামরিক সহকারী।
বৃদ্ধ স্টিমসন বলেন, নিশ্চয়। আপনি তাকে নির্বাচন করুন। তেমন কোনো লোক জানা আছে আপনার?
–আছে স্যার। বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক রবার্ট জে. ওপেনহাইমার।
–তাকে বাজিয়ে দেখুন। যাচাই করুন। ক্লিয়ারেন্সের ব্যবস্থা করুন।
ধন্যবাদ স্যার।
***
যুদ্ধ-সচিব যেমন এককথায় মেনে নিয়েছিলেন, তার অধীনস্থ চিফ অফ স্টাফ জেনারেল মার্শাল কিন্তু তেমনিভাবে এ নির্বাচন মেনে নিলেন না। কে এই রবার্ট জে. ওপেনহাইমার, যাকে জেনারেল গ্রোভসস্ এতবড় সম্মানজনক পদে বসাতে চাইছেন? সে কি নোবেল-লরিয়েট? সে কি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোনো অসামান্য দানের অধিকারী? বয়সে, পদমর্যাদায় সে কি ওই এক ডজন নোবেল-প্রাইজ-পাওয়া ধুরন্ধর বৈজ্ঞানিককে নিয়ে কারবার করতে পারবে? ওই অজ্ঞাতনামা ওপেনহাইমারের বায়োডাটার’ ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে এইসব প্রশ্নের জবাব খুঁজেছিলেন জেনারেল মার্শাল। দুর্ভাগ্যবশত প্রতিটি প্রশ্নের জবাবই হচ্ছিল নেতিবাচক! বায়োডাটা অনুযায়ী।
উনিশ শ চার সালে নিউ ইয়র্কে জন্ম। পিতা জার্মানি থেকে এসেছিলেন সতেরো বছর বয়সে। একজন সাফল্যমণ্ডিত বিজনেসম্যান। মায়ের জন্ম বালটিমোরে। বিবাহের আগে ছিলেন আর্টিস্ট এবং আর্ট-শিক্ষিকা। ওপেনহাইমার 1922-এ হাভার্ড কলেজে ভর্তি হয়, তিন বছর পরে ডিগ্রি পায়। চলে যায় কেমব্রিজে। পরে জার্মানির গোটিনজেন-এ। 1927-এ ডকটরেট পায় সেখান থেকে। তারপর হাভার্ড-এ বছরখানেক ফেলোশিপ পায়, পরে লিডেন ও জুরিখে চাকরি করে। এর পরে ফিরে আসে আমেরিকায়। গত বারো-তেরো বছর সে বার্কলেতে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছে।
অর্থাৎ নেহাত মামুলি কেরিয়ার। বড়জোর বলতে পারা যায়, গড়পড়তা ছাত্রদের চেয়ে কিছু ওপরে। মন্দ নয়-এর ওপর–চলনসই। ওর সমবয়সী এবং সহাধ্যায়ী ছাত্ররা ইতিমধ্যে অনেক-অনেক বেশি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মৌলিক কাজ করেছে, নোবেল পুরস্কার পেয়েছে–যেমন হেইসেনবের্গ, ফের্মি, ডিরাক, জোলিও-কুরি ইত্যাদি ইত্যাদি। অথচ ওপেনহাইমার
জেনারেল মার্শাল শেষ পর্যন্ত ডেকে পাঠালেন গ্রোভসকে। বললেন, আমি দুঃখিত জেনারেল, আপনার সঙ্গে একমত হতে পারছি না। এই ওপেনহাইমার ছোকরাকে দিয়ে আমাদের কাজ চলবে না।
-কেন জেনারেল?
–কী দেখে নির্বাচন করলেন ওকে? এতগুলো নোবেল-লরিয়েটকে
বাধা দিয়ে গ্রোভস্ বলেন, নোবেল-লরিয়েটদের চালাতে হলে নোবেলতর-লরিয়েট চাই এ ধারণা হল কেন আপনার? আমি তো সাধারণ পি. এইচ. ডি.-ও নই, তবু তো বেশ চলছে আমার।
–আপনার কথা আলাদা। আচ্ছা সত্যি করে বলুন তো–কী দেখেছেন আপনি ওই ছোকরার ভিতর?
সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে জেনারেল গ্রোভসস বলেন, আমি ওর চোখে আগুন জ্বলতে দেখেছি জেনারেল!
মার্শাল সামরিক অফিসার, প্র্যাকটিক্যাল মানুষ। প্রাগম্যাটিক! এমন ভাবালুতা কখনও লক্ষ্য করেননি ইতিপূর্বে। আর কোনো প্রশ্ন করেন না উনি। বলেন, ইফ য়ু মাস্ট-ওয়েল, হ্যাভ হিম। প্রোভাইডেড…….
হ্যাঁ, ‘প্রোভাইডেড’! যদি এফ. বি. আই. ওকে ক্লিয়ারেন্স দেয়। এতবড় দায়িত্বপূর্ণ কাজে নিয়োগ করার আগে রাষ্ট্রের গুপ্তচর বাহিনিকে সুযোগ দিতে হবে। তারা চিরে-চিরে ফালাফালা করে দেখবে ওপেনহাইমারের অতীত ইতিহাস। লোকটাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করা যায় কিনা। তাতে অবশ্য গ্রোভস্ রাজি। রাজি হতেই হবে। এই হচ্ছে আইন। স্থির হল, ওপেনহাইমারকে সাময়িকভাবে কাজে বহাল করা হবে। প্রভিশানালি। এফ. বি. আই-য়ের ক্লিয়ারেন্স পেলে তাকে দেওয়া হবে পাকা নিয়োগপত্র।
***
ওপেনহাইমার বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দীর্ঘ দিনের ছুটি নিয়ে এসে যোগ দিল জেনারেল গ্রোভসস-এর দপ্তরে। ছায়ার মতো ঘুরতে লাগল সে বড়সাহেবের সঙ্গে। অচিরে মুগ্ধ হয়ে গেলেন গ্রোভ। ওপির কর্মক্ষমতায়, দৈহিক ও মানসিক সহ্য ক্ষমতায়, উৎসাহে, অধ্যবসায়ে। স্থির করলেন যেমন করেই হোক ওকে কাজে আটকাতে হবে।
গ্রোভস-এর সঙ্গে সব কয়টি কেন্দ্র ঘুরে এসে ওপি বললে, স্যার, দুটো কথা আমার বলার আছে।
-বল?
প্রথমত, আপনি নৌ-বিভাগ এবং বিমানদপ্তরকে এবার ব্যাপারটা জানান। তাদের প্রস্তুত হতে সময় লাগবে। যে পাইলট প্লেনটা উড়িয়ে নিয়ে যাবে, যে বোমাটা ফেলবে তারা ইতিমধ্যে ডামি নিয়ে অভ্যাস শুরু করুক। কোটি-কোটি ডলার খরচ করে যে বোমা তৈরি হবে, ছোঁড়ার দোষে সেটা যেন ব্যর্থ না হয়।
–দ্বিতীয়ত?
–দ্বিতীয়ত, বোমা তৈরির কারখানাটা এবার বানাতে শুরু করা উচিত। পাঁচটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে পারমাণবিক বোমা বানানোর চেষ্টা হচ্ছে–হচ্ছে দশটি কেন্দ্রে। কিন্তু ওঁরা পদ্ধতিটা থিওরেটিক্যালি’ বলবেন। সেটা বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে একটা প্রকাণ্ড তৈরি-কারখানা চাই–
–কিন্তু সে তো দেশের যে কোনো কারখানাতেই হতে পারে ডক্টর?
পারে না স্যার। সেটা হতে হবে জনমানবের বসতি থেকে বহু দূরে, লোকচক্ষুর আড়ালে। বোমার ফর্মুলা যদি আমরা আজ থেকে এক বছর পরে পাই, তবে এই এক বছরের ভিতর আমাদের ফ্যাক্টরি, স্টাফ-কোয়াটার্স, জল-বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি সব কিছু শেষ করে তৈরি হয়ে থাকতে হবে। নয় কি?
গ্রোভস খুশি হলেন। অত্যন্ত খুশি হলেন। বলেন, সত্যি কথা বলতে কি এটা আমিও ভেবেছি। ইতিমধ্যে তিন চারটে সম্ভাব্য ‘সাইট’ ঠিক করেও রেখেছি। চল, আমরা দুজনে সেগুলি দেখে আসি।
সম্ভাব্য স্থানগুলির তালিকা দেখে ওপেনহাইমার বললে, আমি নিশ্চিত–আপনি শেষ পর্যন্ত এই লস অ্যালামসকেই নির্বাচন করবেন।
-কেমন করে জানলে? তুমি গিয়েছ ওখানে?
-ওখানে আমার বাড়ি। ছেলেবেলায় ওখানকার স্কুলে পড়েছি–নিউ মেক্সিকোর রাঞ্চে আমার কৈশোর কেটেছে। জায়গাটা হবে এ কাজের জন্য আইডিয়াল সাইট।
নিউ-মেক্সিকোর এক জনমানবহীন প্রান্তরে অস্তেবাসী জনপদ সান্তা-ফে। সেখানে থেকে একটা উদাসী সড়ক চলে গেছে পাহাড়ের ওপর। ওই পাকদণ্ডী পথের প্রান্তে আছে একটা ছোট্ট স্কুল। 1918 সালে ওই লস অ্যালামস রাঞ্চ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার–আলফ্রেড জে কর্নেল। এখন তিনি অশীতিপর বৃদ্ধ। সংসারে কেউ নেই। ওই স্কুলটা তার প্রাণ। ওপেনহাইমার ঠিক তার ছাত্র নয়, তবু দুজনেই দুজনকে চেনেন। সমুদ্র সমতল থেকে সাত হাজার ফুট ওপরে ভারি সুন্দর পরিবেশে এই স্কুলটি অবস্থিত। মাঝে মাঝে শিকারীরা আসে বন্দুক নিয়ে–ওখানকার পার্বত্য অরণ্যে এখনও প্রচুর হরিণ পাওয়া যায়; আর পাওয়া যায় গেম বার্ডস। শান্ত পরিবেশ বন্দুকের মুহুর্মুহু গর্জনে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সেদিন বৃদ্ধ কর্নেল বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়েন। তারপর শিকারীরা আবার চলে যায়, স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে খেলায়, পড়ায় মেতে ওঠেন বৃদ্ধ।
একদিন ওই স্কুলের সামনে এসে থামল একটা জিপ। নেমে এলেন তিনজন ভদ্রলোক। বেসামরিক লোক। তার মধ্যে ‘ওপি’কে চিনতে পারলেন বৃদ্ধ কর্নেল। বলেন, আরে এস এস। তুমি কী মনে করে? কই বন্দুক আনোনি তো?
–বন্দুক! বন্দুক কী হবে স্যার?
–ও! শিকার করতে আসনি তাহলে? বাল্যভূমি দেখতে এসেছ? তা ভালো। কিন্তু এঁরা?
মিস্টার গ্রোভস, মিস্টার নিকলস্-আমার বন্ধু।
বৃদ্ধ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তার স্কুলটা দেখালেন। ছেলেদের দেখালেন। খুশিয়াল হয়ে উঠলেন তিনি। ওপেনহাইমারের মনের ভিতর তখন কী হচ্ছিল তা কেউ খেয়াল করেনি।
সমস্ত এলাকাটা পরিদর্শন শেষ করে সিভিলিয়ানবেশী তিনজন আবার ফিরে এলেন নিউইয়র্কে। হ্যাঁ, জায়গাটা পছন্দ হয়েছে গ্রোভূ-এর।
সাতদিন পরে আলফ্রেড কর্নেল একটি মর্মান্তিক আদেশ পেলেন। যুদ্ধের প্রয়োজনে তার স্কুল এবং তৎসংলগ্ন সমস্ত জমি, মায় গোটা পাহাড়টা সরকার জবরদখল করছেন। না, ঠিক জবরদখল নয়, খেসারত বাবদ একটা চেকও যুক্ত ছিল পত্রের সঙ্গে। মাথায় হাত দিয়ে বসলেন বৃদ্ধ। এ কী হল? কেমন করে হল? কাকে ধরবেন? কার কাছে দরবার করবেন? আচ্ছা ‘ওপি’কে চিঠি লিখলে কেমন হয়? সে তো এখন মস্ত অধ্যাপক। বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার প্রফেসর!
কিছুতেই কিছু হল না। সব ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হল। ছাত্ররা ফিরে গেল যে যার বাড়ি। লাইব্রেরির বইগুলো বিলিয়ে দিলেন। চেকটা ক্যাশ করতে পাঠালেন ব্যাঙ্কে।
চেক-এর অঙ্কটা বড় জাতেরই ছিল। বৃদ্ধের বাকি জীবনের খোরপোশ চলে যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তার প্রয়োজন হয়নি। চেক ক্যাশ হয়ে আসার আগেই ভগ্নহৃদয়ে আলফ্রেড কর্নেল মারা গেলেন। ঈশ্বরকে ওপেনহাইমার ধন্যবাদ দিয়েছিল কি সেজন্য? বৃদ্ধের মুখোমুখি তাকে দ্বিতীয়বার দাঁড়াতে হল না বলে?
গ্রোভস-এর প্রথমে ধারণা ছিল এখানে শতখানেক বৈজ্ঞানিক এসে হয়তো কাজ করবেন। প্রাথমিক ব্যবস্থা সেই মতোই হয়েছিল। কিন্তু বছর শেষ না হতে ওখানে এলেন সাড়ে তিনহাজার কর্মী, পরের বছর সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়াল ছয় হাজারে।
বিজন প্রান্তরে এমন একটা কারখানা কেন গড়ে উঠছে–কী তৈরি হবে ওখানে, একথা সততই জিজ্ঞাসা করে সকলে। জবাব পায় না। বুঝতে পারে না তারা। ওখানে যারা আসে, থাকে, তারা মিলিটারি পোশাকের নোক নয়, সবই সিভিলিয়ান।
***
চূড়ান্ত গোপনীয়তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল লস-অ্যালামস-এ। প্রতিটি বৈজ্ঞানিকের একটা করে নামকরণ করা হল। সেই নতুন নামে তাদের চিঠিপত্র আসত। আসত একই ঠিকানায়—’ইউনাইটেড স্টেট আর্মি, পোস্ট অফিস বক্স নং 1663’-এই ঠিকানায়। লস অ্যালামস তো দূরের কথা, খামের ওপর নিউ-মেক্সিকো পর্যন্ত লেখা হত না। প্রতিটি বৈজ্ঞানিকের ব্যক্তিগত চিঠি আসা এবং যাওয়ার পথে সেনসর করা হত। কোনো গোপন খবর যেন কোনোভাবে বাইরে পাচার হয়ে যায়। অধিকাংশ বিজ্ঞানী স্ত্রী-পুত্র পরিজনদের ছেড়ে এসেছেন। তারা শুধু জানতেন স্বামী যুদ্ধের গোপন-কাজে নিযুক্ত। কী কাজ, কোথায় কাজ তা জানতেন না। বিজ্ঞানীদের কড়া হুকুম দেওয়া হয়েছিল পরস্পরকে যেন ‘ডক্টর’ বা ‘প্রফেসর’ জাতীয় সম্বোধন না করেন। এতে সন্দেহের উদ্রেক করবে। তাহলে রাম-শ্যাম-যদু ভাবতে বসবে–এতগুলি পি. এইচ. ডি. অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এই বিজন প্রান্তরে কেন জমায়েত হয়েছেন? হয়তো গোটা পরিকল্পনাটাই তাতে বানচাল হয়ে যাবে! সম্বোধন করতে হবে শুধু ‘মিস্টার’ বলে। অনেকের সেটা ভুল হয়ে যেত। অধ্যাপকসুলভ অন্যমনস্কতায় ভুল সম্বোধন করেই মনে মনে জিব কাটতেন! একবার এডওয়ার্ড টেলর সান্তা-ফেতে একটি মর্মর মূর্তি দেখিয়ে তার বন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন–ওটা কার মূর্তি?
বন্ধু অ্যালিসনও পদার্থবিজ্ঞানী। রসিক ব্যক্তি। তিনি টেলরের কানে কানে বললেন, মূর্তিটা আর্চবিশপ লামির। কিন্তু খবরদার–তোমাকে যদি কেউ এ প্রশ্ন করে তবে বলবে ‘মিস্টার’ লামির। ভুলেও আর্চবিশপ’ বোলো না যেন!
সরল প্রকৃতির টেলর অবাক হয়ে বলেন, কেন? পাথরের মূর্তিতে আবার গোপনীয়তা কিসের?
অ্যালিসন বিজ্ঞের হাসি হেসে বলেন, আছে, ব্রাদার, আছে! বুঝলে না? নাহলে রাম-শ্যাম-যদু ভাবতে বসবে, এতগুলি কাক কেন প্রত্যহ ওঁর মাথায় ‘ইয়ে’ ত্যাগ করে। খ্রিস্টধর্মটাই হয়তো বানচাল হয়ে যাবে!
বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক নীলস বোহর-এর নতুন নাম দেওয়া হল ‘নিকোলাস বেকার। বাঘা বাঘা ফমূলা ওঁর কণ্ঠস্থ অথচ এই নামটা তার মনে থাকত না। মিটিং-এর ভিতর কেউ হয়তো প্রশ্ন করে ওঠে–মিস্টার বেকার এ বিষয়ে কী বলেন?
বোহর নির্বিকারভাবে ব্যোম মেরে বসে থাকেন। ওঁর কোনো ছাত্র তখন হয়তো ওঁর কানে কানে বলে, স্যার, আপনাকেই প্রশ্ন করা হচ্ছে–
প্রফেসর আঁৎকে উঠতেন, হু? মি? গুড হেভেন্স! আমার মনেই থাকে না যে আমার নাম বোহর নয়, বেকার!
অতঃপর মিটিং-এ উপস্থিত আর কারও জানতে বাকি থাকে না ‘নিকোলাস বেকার’ কার ছদ্মনাম!
***
আর একবার। সেটা নিউ ইয়র্কে। প্রফেসর বোহর একটা অত্যন্ত জরুরি ও গোপনীয় মিটিং-এ যোগদান করতে যাচ্ছেন। অন্যমনস্ক অধ্যাপকটির জন্য সদা-সর্বদা একজন দেহরক্ষীর ব্যবস্থা ছিল। সিকিউরিটি-ম্যান। গন্তব্যস্থলে ও পৌঁছে দিয়ে লোকটা বিদায় নিল। মিটিং-এ বেচারি যেতে পারবে না। লিফ-এ মুখে ওঁকে রেখে শেষবারের মতো ফিসফিস করে মনে করিয়ে দেয়; প্লি প্রফেসর, মনে রাখবেন আপনার নাম নীলস বোহর নয়, নিকোলাস বেকার। কেমন?
-ঠিক আছে। ঠিক আছে! আমি অত অন্যমনস্ক নই! আমি ভুলিনি!
লিফট এসে দাঁড়াল। ওঁর সঙ্গে একই লিফট-এ উঠেছেন একটি মহিলা : স্বয়ংক্রিয় লিস্ট। চালক নেই। তৃতীয় যাত্রীও নেই। রুদ্ধদ্বারকক্ষে একটি মহিলা সহযাত্রী দেখে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হয়ে কোণ নিলেন অধ্যাপকমশাই। মহিলাটি এঁকে আদৌ নজর করেননি। একমনে একটা খবরের কাগজ দেখছেন তিনি। হঠাৎ প্রফেসর বোহর-এর মনে হল মহিলাটি তার অত্যন্ত পরিচিত। আরে! এ যে হালবানের স্ত্রী। হালবান ছিলেন ডেনমার্কে ওঁর সহকর্মী। প্রফেসর সবিনয়ে প্রশ্ন করেন :
–মাপ করবেন, আপনি কি ফ্রাই ফন হালবান নন?
নীলস বোহর জানতেন না, তার বন্ধু হালবানের সঙ্গে স্ত্রীর বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গেছে এবং মহিলাটি মিস্টার প্লাজেককে ইতিমধ্যে বিবাহ করেছেন। ভদ্রমহিলা কাগজ থেকে মুখ না তুলে বললেন, আজ্ঞে না! আপনার ভুল হচ্ছে স্যার আমার নাম মিসেস প্লাজেক।
–আয়াম সরি!
লিফট ওপরে উঠছে। হঠাৎ কাগজ থেকে মুখ তুলে মহিলাটি তার সহযাত্রীর দিকে চোখ তুলে চাইলেন। একেবারে লাফিয়ে ওঠেন তিনি। বলেন, কী আশ্চর্য! আপনি! প্রফেসর বোহর!
প্রফেসর বোহর গম্ভীরভাবে বললেন, আপনার ভুল হয়েছে মাদাম–আমার নাম নিকোলাস বেকার!
লিফট পৌঁছে গেল! গটগট করে এগিয়ে গেলেন নিকোলাস বেকার। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন মিসেস প্লাজেক! ঋষিপ্রতিম প্রফেসর বোহর এমন বেমক্কা মিথ্যা কথা বললেন কেন?
.
০৮.
অশান্তভাবে নিজের ঘরে পদচারণা করছিলেন জেনারেল গ্রোভসস। ওপিকে ডেকে পাঠিয়েছেন অনেকক্ষণ। এখনও আসছে না কেন সে? কিন্তু এলে তিনি কী বলবেন? কেমন করে জেনে নেবেন প্রকৃত সত্যটা? ওপি, ওপেনহাইমারকে তার চাই,–নিতান্তই অপরিহার্য সে। এই কয়েকমাসে সে মন্ত্রের মতো সমস্ত প্রকল্পটাতে যেন প্রাণ সঞ্চার করেছে। তার অধ্যবসায়ে, কর্মপদ্ধতিতে, তার উৎসাহে অভিভূত হয়ে পড়েছেন গ্রোভস, এখন তাকে কোনক্রমেই ছাড়া যায় না। অথচ
হ্যাঁ। এফ. বি. আই. থেকে রিপোর্ট এসেছে ইতিমধ্যে। গুপ্তচর দপ্তর স্পষ্ট করে জানিয়েছে, বার্কলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রবার্ট জে ওপেনহাইমারকে সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স দেওয়া যাবে না। তিন-তিনটি ছিদ্র তারা বার করেছে ওপির পূর্ব-ইতিহাস হাড়ে। এক নম্বর, সে দীর্ঘদিন ধরে কম্যুনিস্ট চিন্তাধারা প্রচার করত। দু নম্বর, ওর ভ্রাতৃবধূ ‘জ্যাকি’ একজন কম্যুনিস্ট ছিল। আর তিন নম্বর, ওর স্ত্রীর প্রথমপক্ষের স্বামী ছিল একজন উৎসাহী কম্যুনিস্ট কর্মকর্তা।
গ্রোভস্ টেবিলের ওপর থেকে একখানি পত্রিকা তুলে পাতা উল্টাতে থাকেন। ‘পিপলস ওয়ার্ল্ডের’ বর্তমান সংখ্যা। পত্রিকাটির নামই শোনা ছিল না। রিপোর্টখানা পড়ে কৌতূহলের বশে আজ একখানা কিনে ফেলেছেন। পাতা উল্টে দেখছিলেন, কই তেমন কোনো মারাত্মক রচনা তো নজরে পড়ল না?
–গুড মর্নিং স্যার!–ওপি এসেছে।
–এস, বস বস।
ভিজিটার্স চেয়ারে বসতে বসতে ওপেনহাইমার বলে, এ কি স্যার? আপনার হাতে পিপল্স ওয়ার্ল্ড!
-কেন? এটা কি নিষিদ্ধ কোনো পত্রিকা?
–না। নিষিদ্ধ ঠিক নয়, তবে ওরা তো ডেমোক্রেসিতে বিশ্বাস করে না—
–তাই নাকি? আমি পড়ে দেখিনি। তুমি পড়েছ?
–এ সংখ্যাটা পড়িনি। বস্তুতপক্ষে গত তিন-চার বছর পড়িনি। তবে এককালে আমি ওই পত্রিকার সভ্য ছিলাম।
-তাই নাকি?
–শুধু তাই নয় স্যার, ছদ্মনামে এককালে আমি ওতে প্রবন্ধও ছাপিয়েছি! স্তম্ভিত হয়ে গেলেন গ্রোভস্। এ খবরটা তো এফ. বি. আই.ও পায়নি। অথচ ও কেমন সরল বিশ্বাসে বলে গেল! পুনরায় প্রশ্ন করেন, সে সময় তোমার বুঝি ক্যমুনিজম-এ বিশ্বাস ছিল?
–তা ছিল। কিছুটা আমার ভাইয়ের প্রভাব—
ভাই! ভাই কে?
–আমার ভাই ফ্রাঙ্ক ছিল ঘোর কম্যুনিস্ট। তার স্ত্রী জ্যাকলিনও তাই। এখন অবশ্য তাদের মত বদলে গেছে। যাই হোক, আমাকে ডেকেছিলেন কেন?
মনের মেঘ অনেকখানি সরে গেছে ইতিমধ্যে। গ্রোভস্ শেষ প্রশ্নটা এড়িয়ে বলেন, কিছু মনে কর না ওপি, তোমাকে একটি পারিবারিক প্রশ্ন করছি। তোমার স্ত্রীর প্রাক্তন স্বামীও কি একজন কম্যুনিস্ট ছিলেন?
–ছিলেন। তাঁর নাম জো ড্যালবর। তিনি ছিলেন স্পেনের একজন নেতৃস্থানীয় কম্যুনিস্ট পার্টি অফিশিয়াল। স্পেনের গৃহযুদ্ধে তিনি মারা যান।
–তার মানে তোমার স্ত্রীও কিছুটা
–কিছুটা কেন? এককালে তিনিও ঘোর কম্যুনিস্ট ছিলেন।
একটু ঘুরিয়ে গ্রোভস বললেন, আমি ভাবছি–এসব কথা আবার এফ. বি. আই. খুঁচিয়ে বের করবে না তো? তুমি তো জানই, এফ. বি. আই.-এর ক্লিয়ারেন্স ছাড়া
–হ্যাঁ, জানি বই কী! কিন্তু খুঁচিয়ে বার করার কী আছে? আমাকে প্রশ্ন করলেই আমি অকপটে সব বলব। এককালে কম্যুনিস্ট ডকট্রিন আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল একথা স্বীকার করতে আমার দ্বিধা নেই। কিন্তু বর্তমানে আমি ডেমোেক্রাসির পূজারী। শুধু আমি নই–আমরা সবাই। আমি, আমার স্ত্রী, আমার ভাই, তার স্ত্রী!
সে যাই হোক আমাকে ডেকেছিলেন কেন?
‘কেন ডেকেছিলেন’ তার কৈফিয়ৎ গ্রোভস কী দিয়েছিলেন, আদৌ দিয়েছিলেন কিনা তার কোনো প্রমাণ নেই। যা আছে তা হচ্ছে সমর বিভাগের একটি গোপন নথি। ওই জুলাই-এর বিশ তারিখে লেখা। চিঠিখানা হুবহু অনুবাদ করে দিলাম–
গোপনতম পত্র
যুদ্ধবিভাগ
চিফ ইঞ্জিনিয়ার দপ্তর
ওয়াশিংটন, জুলাই 20, 1943
বিষয় : জুলিয়াস রবার্ট ওপেনহাইমার
প্রাপক : দ্য ডিস্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ার, মানহাটান ডিস্ট্রিক্ট
স্টেশন ‘এফ’, নিউ ইয়র্ক।
পনেরই জুলাই তারিখে প্রদত্ত আমার মৌখিক নির্দেশের পরিপূরক হিসাবে এতদ্বারা অনুরোধ জানানো যাইতেছে যে, উপরুল্লিখিত ব্যক্তিকে অবিলম্বে প্রস্তাবিত পদে নিযুক্ত করা হউক। ইহাও উল্লেখ থাকে যে, তাহার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ ইতিপূর্বে আপনি আমাকে জানাইয়াছেন তাহা পাঠান্তে সম্পূর্ণ নিজ দায়িত্বে বিশেষ ক্ষমতাবলে আমি এই আদেশ জারি করিতেছি। উল্লিখিত ব্যক্তি এই প্রকল্পের পক্ষে অনিবার্য।
— এল, আর. গ্রোভস
ব্রিগেডিয়ার-জেনারেল, সি, ই,
তরোয়ালের এক কোপে সব রকম বাধাবিঘু সরিয়ে দিলেন সামরিক অফিসারটি।
ওপি হলেন লস-অ্যালামসের অফিশিয়াল কর্ণধার!
***
লস অ্যালামসে একে একে এসে জুটলেন বিজ্ঞানীরা। মূল-নিয়ামক ওপি। পৃথিবীর ইতিহাসে এতগুলি প্রথমশ্রেণির বৈজ্ঞানিক কখনও একত্র হয়ে একযোগে কাজ করেননি। এলেন–ৎজিলাৰ্ড, গ্যামো, টেলার, উইগনার, ফের্মি, হান্স বেথে,–ফন নয়মান, ক্রিস্টিয়াকৌস্কি, রোবিনোভিচ, ওয়াইস্কফ, পার্লস, অটো ফ্রিশ, উইলিয়াম পেনি, ক্লাউস ফুকস, কেনেডি, স্মিথ, পার্সন ইত্যাদি ইত্যাদি এবং ইত্যাদি। সাতটি বিভাগ, তার সাতজন কর্ণধার–প্রত্যেকের অধীনে পাঁচ-সাতটি শাখা। থিওরিটিক্যাল বিভাগের এনরিকো ফের্মি–প্রভৃতি প্রভৃতি এবং প্রভৃতি। সকলের পরিচয় দিতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। দু-চার জনের কথা বলি–
হান্স বেথে নোবেল-লরিয়েট জার্মান। নাৎসি শাসনে উত্যক্ত হয়ে 1935-এ পালিয়ে আসেন আমেরিকায়। তাঁর জীবনের এক কৌতুককর অভিজ্ঞতার কথা বলি–যা থেকে বোঝা যাবে, বিজ্ঞানীরা রাজনীতিকদের পাল্লায় পড়ে কী জাতীয় নাকাল হতেন। পারির পতনের সময়ে (1940) আমেরিকায় উদ্বাস্তু হ্যান্স বেথে একটি সমর-সম্বন্ধীয় আবিষ্কার করে বসলেন। কামানের গোলায় সাঁজোয়া গাড়ির প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থার বিষয়ে একটি আবিষ্কার। কাগজপত্র নিয়ে তিনি দেখা করলেন মার্কিন সামরিক বড়কর্তার সঙ্গে। সামরিক বড়কর্তা সেটা পড়ে অভিভূত হয়ে বললেন, প্রফেসর, আপনার এ আবিষ্কার প্রভূতভাবে আমাদের কাজে লাগবে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ!
হান্স বেথে গদগদ হয়ে বলেন, কিছু না, কিছু না–আমার পরীক্ষা কার্যটা শেষ হয়নি। আরও উন্নত ধরনের সাঁজোয়া গাড়ির চাদর তৈরি করব আমি। রিসার্চের কাগজগুলো দিন–অসমাপ্ত কাজটা শেষ করি–
বড়কর্তা বললেন, আমি অত্যন্ত দুঃখিত প্রফেসর, রিপোর্টটা আর আপনাকে ফেরত দেওয়া যাবে না। আমাদের চোখে আপনি হচ্ছেন শত্রুপক্ষের লোক, জার্মান ন্যাশনাল!
–সে কি! আবিষ্কারটা যে আমারই! আর ওটা যে অসম্পূর্ণ!
–আয়াম সরি, প্রফেসর!
—দুত্তোর ‘সরি’! ওর কপিও যে নেই আমার কাছে –
আয়াম সরি এগেন, হের প্রফেসর!
পাঠকের হয়তো মনে হচ্ছে আমি বানিয়ে বলছি! বিশ্বাস করুন-এতে একবিন্দু অতিরঞ্জন নেই। সেই হান্স বেথে বর্তমানে লস অ্যালামসের থিওরিটিক্যাল ডিভিশনের ডিরেক্টর।
***
এক্সপ্লোসিভ বিভাগের ডিরেক্টার জর্জ ক্রিস্টিয়াকৌস্কি-সংক্ষেপে ‘কিস্টি। খাস রাশিয়ান। বয়স তেতাল্লিশ। জন্ম কিয়েভ-এ। বলশেভিকদের বিরুদ্ধে শ্বেত রাশিয়ান বাহিনির হয়ে কৈশোরে লড়াই করেছিলেন। তুরস্কের ভিতর দিয়ে পালিয়ে শেষ পর্যন্ত কপর্দকহীন উদ্বাস্তু হিসাবে এসে পৌঁছান বার্লিনে। সেখানে দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি নেন; 1925-এ চলে আসেন মার্কিন-মুলুকে। প্রিন্সটনে অধ্যাপনা করছিলেন-ওপি তাকে ধরে এনেছে লস অ্যালামসে। দুর্ধর্ষ বেপরোয়া এই কিস্টি। একবার তিনি তার সহকর্মীদের বলেছিলেন, তোমরা বোমার এই বিস্ফোরকগুলোকে খামকা ভয় পাও। ডিনামাইট নয় এই প্যাকেটগুলো–নাড়াচাড়ায় ফেটে যাবে না। অত পুতুপুতু কর কেন?
ওঁর সহকর্মীরা সৌজন্যবোধে মাথা নাড়ে। বেশ বোঝা যায়, তারা মেনে নেয় না ওঁর কথা।
প্র্যাকটিক্যাল কিস্টি বুঝতে পারেন–ওরা বিশ্বাস করছে না। তৎক্ষণাৎ আদেশ দিলেন বিস্ফোরক-ভর্তি প্যাকিং কেসগুলো ওঁর গাড়িতে তুলে দিতে। আট-দশটা প্যাকিং-কেস গাড়ির সিটে চড়িয়ে কিস্টি বিস্মিত সহকর্মীদের চোখের সামনে দিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কোথায় গেলেন উনি?–ভাবছে সবাই। কোথাও যাননি কিস্টি। সামনের উবড়ো-বড়ো মাঠের মাঝখানে খানিকটা বেপরোয়া ড্রাইভ করে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরে এলেন এক্সপ্লোসিভ বিভাগের ডিরেক্টার। চোখ বড় বড় করে দাঁড়িয়ে আছে সহকর্মীরা। কিস্টি গাড়ি থেকে নেমে এসে বললেন, দেখলে? ফাটলো? নাও, এবার গাড়ি থেকে ওগুলো নামাও!
আর এক রাশিয়ান বৈজ্ঞানিক হচ্ছেন গ্যামো–জর্জ গ্যামো। যাঁর “One? Two? Three… Infinity” বইটি বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য। চুটকি রসিকতায়, গল্প বলায়, ধাঁধা বানানোতে অদ্ভুত পারদর্শিতা ছিল তাঁর। জন্ম রাশিয়ায় শিক্ষা গোটিনজেন-এ। হেইসেনবের্গ, ওপি, টেলার ইত্যাদির সহপাঠী। গ্যামো কীভাবে রাশিয়া থেকে পালিয়ে আসেন তার গল্প শুনিয়েছেন উনি। স্কুলের গণ্ডী তখন সবে পার হয়েছেন গ্যামো। ছুটিতে উনি জার্মানি বেড়াতে যাবার সংকল্প করলেন-বাসনা, স্বচক্ষে দেখে আসবেন সেই অদ্ভুত মানুষটিকে–আলবার্ট আইনস্টাইন যাঁর নাম। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় গ্যামো অঙ্কে রেকর্ড মার্ক পেয়েছেন–ওইটাই তার প্রাইজ হিসাবে দাবি করলেন। বাবা রাজি হলেন খরচ দিতে–রাজি হলেন না রাশিয়ান গভর্নমেন্ট। সেইদিন থেকেই গ্যামোর স্বপ্ন ছিল রাশিয়া থেকে পালানো। আফগান-সীমান্ত দিয়ে প্রথমবার পালাবার চেষ্টা ব্যর্থ হল। সীমান্তরক্ষীরা ধরে ফেলল কিশোরবয়স্ক পলাতককে; কিন্তু গ্যামো তাদের বুঝিয়ে দিলেন, তিনি ছুটিতে বেড়াতে এসেছেন। ওই পাহাড়ের মাথায় চড়বার বাসনা নিয়ে বাড়ি থেকে বার হয়ে পথ হারিয়েছেন। যাই হোক, তাকে ফিরে আসতে হল। এরপর অল্পবয়সেই গ্যামো বিবাহ করেন। সদ্যবিবাহিতা বধূকে খুলে বললেন মনের কথা। অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধে কিশোরী মেয়েটি রাজি হয়ে যায়। একটা নৌকা নিয়ে দুজনে বার হয়ে পড়েন একদিন কৃষ্ণসাগরের বুকে। ওপারে রাশিয়ান এলাকা নয়। এই দুঃসাহসিক অভিযানটিও ব্যর্থ হল। ঝড়ের মধ্যে পড়ে এই দুলর্ভ প্রতিভার সলিল-সমাধি হতে বসেছিল। উদ্ধার করল আবার সেই সীমান্তরক্ষীর দল। রাশিয়ান বর্ডার-পুলিস। এবারও তার আসল উদ্দেশ্য তারা বুঝতে পারেনি। কিন্তু ‘ওয়ান, টু, থ্রি.ইনফিনিটি’ গ্রন্থ যিনি ভবিষ্যতে লিখবেন তিনি কি প্রথম আর দ্বিতীয়বার ব্যর্থ হয়েই থামতে পারেন? ইনফিনিটি পর্যন্ত যেতে হয়নি, তৃতীয় প্রচেষ্টাতেই সাফল্যমণ্ডিত হন। এসে পৌঁছালেন বার্লিনে। দেখলেন সেই মানুষটিকে, বিংশ শতাব্দীর বিস্ময়–আলবার্ট আইনস্টাইনকে!
***
লস-অ্যালামসের আর একটি অদ্ভুত চরিত্র ডক্টর ক্লাউস ফুকস্ (1912-1988)। জার্মান, কিন্তু ইহুদি নন। তবু বিতাড়িত হয়েছিলেন নাৎসি জার্মানি থেকে। কপর্দকহীন অবস্থায় এসে পৌঁছান ইংল্যান্ডে (1933)। বাবা ছিলেন শান্তিকামী প্রটেস্টান্ট ধর্মযাজক–সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। স্পষ্টবক্তা এবং নির্ভীক। তিনি ছিলেন বিশ্বভ্রাতৃত্বের পূজারী, ক্রিশ্চিয়ান কোয়েকার্স-সম্প্রদায়ের একজন কর্মকর্তা! একটি কোয়েকার্স-পরিবারেই আশ্রয় পান ক্লাউস, ইংল্যান্ডে। সাতে-পাঁচে থাকতেন না, রাজনীতি থেকে শত হস্ত দূরে থেকে পড়াশুনা শেষ করলেন ইংল্যান্ডে এসে। দুর্দান্ত ভালো রেজাল্ট হল শেষ পরীক্ষায়। ম্যাক্স বর্ন ওই সময়ে ইংল্যান্ডে–তিনি ক্লাউসকে দেখে আকৃষ্ট হলেন। জুটিয়ে দিলেন এক রিসার্চ স্কলারশিপ। সেখানেও সুনাম হল। পরে জেমস্ চ্যাডউইকের নেতৃত্বে ইংল্যান্ড থেকে যে বৈজ্ঞানিক দল অ্যাটম-বোমা প্রকল্পে আমেরিকায় আসে তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে অটো ফ্রিশ (শ্রীমতী মাইটনারের সেই বোনপো, যিনি নীলস বোহর-এর ঘুষি খেয়েছিলেন), উইলিয়াম পেনি, পার্লস প্রভৃতির সঙ্গে এখানে আসেন। প্রথমে ছিলেন ওক-রিজ-এর গ্যাসীয় ডিফুশন প্রকল্পে। পরে চলে আসেন লস-অ্যালামসে। প্রচণ্ড স্মোকার, মদ্যপানও করেন প্রচুর, তবে মাতাল হন না। ব্যাচিলার, সুদর্শন–মেয়েমহলে খুবই জনপ্রিয়।
মেয়ে-মহলের কথাই যখন উঠল তখন বলি–ডক্টর ফুকস সম্বন্ধে লস-অ্যালামসে একটা গুজব বেশ চালু ছিল। তার সঙ্গে নাকি মিসেস্ অটো কার্ল-এর একটু বিশেষ জাতের সদ্ভাব ছিল। এমন গুজব তো রটতেই পারে। প্রথম কথা, ডক্টর ফুকস্ সুদর্শন, ব্যাচিলার এবং প্রফেসর অটো কার্ল বৃদ্ধ অথচ তাঁর দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী রোনাটা কার্ল ডাকসাইটে সুন্দরী এবং যুবতী। কর্তা-গিন্নিতে না-হোক বিশ-বাইশ বছরের ফারাক! ডক্টর ফুকস্ এবং রোনাটা কার্ল দুজনেই স্বীকার করতেন ওঁরা দুজনে বাল্যবন্ধু। কিশোরী বয়স থেকেই রোনাটা চিনতো ফুকসকে। বস্তুত জার্মানি থেকে পালিয়ে এসে ফুস্ ওই রোনাটাদের পরিবারেই আশ্রয় পায়। আলাপটা সেই আমলের, কিন্তু দুষ্টু লোকের মন তাতে মানে না। তারা ভাবে–এর পিছনে বুঝি গভীরতর এক গোপন ইতিহাস আছে–যার রেশ আজও মেটেনি।
লস-অ্যালামসে–বস্তুত গোটা মানহাটান প্রকল্পে–ডক্টর ফু-এর একটা প্রকাণ্ড দান আছে–উনিই পরমাণু বোমার ক্রিটিক্যাল-সাইজটা অঙ্ক কষে বার করেন। সেই ‘ক্রিটিক্যাল সাইজ’-এর হিসাব এখনও ছাপা হয়নি। সেটা আজও চরমতম গোপন নথি।
***
কিন্তু ক্রিটিক্যাল সাইজটা কী?
ধরা যাক একটা ছোট্ট ইউ-235-এর টুকরোয় কোনো নিউট্রন আঘাত করে একটি পরমাণু বিদীর্ণ করল। তা থেকে নূতন দু-তিনটি নিউট্রন জন্মলাভ করবে এবং দু-তিন দিকে যাবে। ইউ-235-এর টুকরোটা আকারে ছোটো হলে নব-বিমুক্ত নিউট্রন দুটি হয়তো কিছুদূর গিয়েই থেমে যাবে, অর্থাৎ নূতন পরমাণু-অন্তর বিদীর্ণ করার আগেই তার যাত্রা শেষ করবে। এখন যদি আর একটু বড় মাপের টুকরো নিই তাহলে হয়তো একটা থেকে দুটো, দুটো থেকে চারটে নিউট্রন পাব। হয়তো শেষে ওই চারটে নিউট্রনও মাঝপথে বিলুপ্ত হবে। এমনিভাবে বাড়তে বাড়তে আমরা এমন একটা নির্দিষ্ট আকারে পৌঁছাব যখন ওই চেন-রিয়্যাকশান বা ‘চক্রাবর্তন-পদ্ধতি’ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। সেই নির্দিষ্ট মাপকাঠিকেই বলে ‘ক্রিটিক্যাল-সাইজ। লস-অ্যালামসের বিজ্ঞানীরা চাইছিলেন ক্রিটিক্যাল-সাইজের চেয়ে একটু ছোট মাপের দুটি ইউরেনিয়াম টুকরোকে একটা বাধাদানকারী পদার্থের দু-পাশে রাখতে। যদি এমন হয় যে, আকাশ থেকে বোমা পড়তে পড়তে পর্দাটা গলে যাবে, তাহলে ভূপৃষ্ঠে পোঁছবার আগেই দুটি ‘সাব-ক্রিটিক্যাল’ টুকরো পরস্পরের সংস্পর্শে এসে ‘সুপার-ক্রিটিক্যাল’ হয়ে যাবে। যার অর্থ প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। এই ব্যাপারটা চিত্র 9-এ বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে।
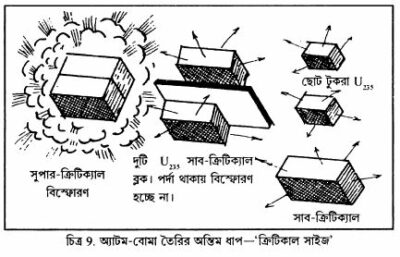
[চিত্র 9. অ্যাটম-বোমা তৈরির অন্তিম ধাপ- ‘ক্রিটিকাল সাইজ’]
***
কিন্তু লস-অ্যালামসে সবচেয়ে অদ্ভুত চরিত্র হচ্ছেন রিচার্ড ফাইনম্যান (1918 – 1988)। ডাক নাম ‘ডিক’। সব রিচার্ড-এরই ডাকনাম হয় ডিক, যেমন সব কানাইলালের ডাক নাম কানু। ফাইনম্যানের আর এক ডাক নাম চালু হয়েছিল লস-অ্যালামসে–মসকুইটো বোট। ডিরেক্টার নোবেল-লরিয়েট হান্স বেথে সেই সুবাদে হচ্ছেন ‘ব্যাটলশিপ’! মানসাঙ্কে ফাইনম্যান ছিলেন ফের্মির মতো ধুরন্ধর। কাউকে কেয়ার করতেন না। নোবেল-প্রাইজপ্রাপ্ত বেথে, ফ্রাঙ্ক, লরেন্স ইত্যাদিকে মুখের ওপর বলতেন-‘কী বকছেন স্যার পাগলের মতো!’–’পাগলের মতো’ কথাটা ছিল তার প্রতিবাদের বাঁধা লবজ, মুদ্রাদোষ!
অদ্ভুত ফুর্তিবাজ। দুষ্টমিতে ভরা। একেবারে ছেলেমানুষ। এদিকে ধাঁধায় পাকা মাথা। ফাইনম্যানের স্ত্রী থাকতেন নিউইয়র্ক। যেমন স্বামী তেমন স্ত্রী। ভদ্রমহিলারও মাথা খেলত ধাঁধার সমাধানে। স্বামী-স্ত্রী নানান ধরনের ধাঁধা নিয়ে সময় কাটাতেন। এখন দুজনে আছেন দেশের দুই প্রান্তে–তাই দুজনে চিঠিপত্র লিখতেন সাঙ্কেতিক ভাষায়। অথবা চিঠি লিখে কুচিকুচি করে ছিঁড়ে পাঠাতেন। ‘জিগস’ ধাঁধার মতো টুকরা কাগজগুলি সাজিয়ে প্রাপককে পাঠোদ্ধার করতে হত। শোনা যায়, এ কাজের উদ্দেশ্য হল সেনসারকে নাকাল করা। ব্যাটারা কেন খুলে পড়বে ওঁদের প্রেমপত্র?
সেনসরের কথাই যখন উঠল তখন বলি শুনুন। সেনসরের বড় কর্তা ম্যাককিলভির সঙ্গে একবার খুব বেধে গিয়েছিল ফাইনম্যানের। ম্যাককিলভি বলে, সাঙ্কেতিক ভাষা ডি-কোড করা অপরাধ-বিজ্ঞানের একটা বিশেষ শাখা। ও-বিষয়ে যে গবেষণা করেনি তার পক্ষে এ ধাঁধার সমাধান সম্ভবপর নয়। ফাইনম্যান বলেছিলেন, লুক হিয়ার ম্যাক্, অপরাধ-বিজ্ঞানী কোনোদিনই অঙ্কশাস্ত্রের মামুলি কোনো ছোট্ট ফর্মুলাও বুঝতে পারবে না, যেমন ধরুন অতি ছোট্ট একটি ফর্মুলা : E = mc^2! কিছু বুঝলেন? অথচ দুরূহতম ক্রিমিনোলজির সমস্যা নিয়ে আসুন আমার কাছে, এক সেকেন্ডে তা ‘ফুস’–
হাতের তুড়ি বাজিয়ে ‘ফুসটা’ যে কতটা অকিঞ্চিৎকর তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন।
ম্যাককিলভি সে অপমান ভোলেনি। দুদিন পরেই সে এসে হাজির হল একখানা চিঠি হাতে। বললে, এক্সকিউজ মি স্যার। এ চিঠি পাস হবে না!
ফাইনম্যান দেখলেন তার স্ত্রীকে লেখা প্রেমপত্রখানা খামখোলা অবস্থায় নিয়ে এসেছে ম্যাককিলভি।
কী ব্যাপার? দেখা গেল–ফাইনম্যান স্ত্রীকে লিখেছিলেন, ‘সাত হাজার ফুট উঁচুতে থাকায় নিউ মেক্সিকোর গরমটা আমরা টের পাচ্ছি না।
ম্যাককিলভি এক গাল হেসে বলে, E = mc ফর্মূলা না বুঝলেও এটুকু বুঝি, এইভাবে আপনি মিসেসকে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, আপনি বর্তমানে অছেন নিউ মেক্সিকোতে। একটা রিলিফ-ম্যাপ খুলে মিসেস্ সহজেই বুঝবেন সাত হাজার ফুট উঁচুতে কোথায় আছেন আপনি! ওই লাইনটা কেটে দিতে হবে।
দুরন্ত ক্রোধে ওর হাত থেকে চিঠিখানা ছিনিয়ে নিয়ে ফাইনম্যান কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। হাসতে হাসতে ফিরে গেল ম্যাককিলভি।
কিন্তু আবার তাকে আসতে হল। এবারও তার হাতে ফাইনম্যানের স্ত্রীকে লেখা চিঠি। এবার ফাইনম্যান স্ত্রীকে লিখেছেন “RETEP” কেমন আছে? SBM OBMOTA এ বছর এসে পৌঁছতে পারবেন বলে মনে হয় না।” পড়ে মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেনি ম্যাককিলভি। Retep অথবা Sbm. Obmota কারও নাম হয় নাকি? চিঠিখানা নিয়ে তাই সে আবার এসেছে ওঁর দপ্তরে। বললে, মাপ করবেন প্রফেসর ফাইনম্যান, এমন অদ্ভুত নাম আমি জীবনে শুনিনি…
প্রচণ্ড ধমক দিয়ে ওঠেন ফাইনম্যান, একজ্যাক্টলি। আমিও তো তাই বলতে চাই! এমন অদ্ভুত নাম আমি জীবনে শুনিনি! প্রফেসর ফাইনম্যান। কে তিনি? আমার নাম মিস্টার হেইলি!
থতমত খেয়ে ম্যাককিলভি বলে, না…ইয়ে…এখানে তো বাইরের লোক কেউ নেই…
–বাইরের লোক নেই এই অজুহাতে আপনি আমাকে ‘প্রফেসর ফাইনম্যান’ বলে ডাকবেন? If you call me such ‘names’ I’ll report against you!
একেবারে মিইয়ে যায় বেচারি। বলে, আমি দুঃখিত। আচ্ছা আচ্ছা মিস্টার হেইলি! কিন্তু আপনার চিঠির অর্থ যে আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।
ফাইনম্যান গম্ভীরভাবে বলেন, প্রেমপত্রটি আপনার উদ্দেশ্যে আমি লিখিনি মশাই। আপনি না বুঝলেও চলবে।
ম্যাককিলভি তবু অনুনয়ের সুরে বলে, তবু স্যার না বুঝে কেমন করে চিঠি। পাস করি বলুন? এই দুটো কথা–Retep এবং Sbm. Obmota-এর অর্থ কি?
এতক্ষণে রাগ পড়ে গেছে ফাইনম্যানের। বললেন, অক্ষরগুলো উল্টোপাল্টা করে সাজানো আছে। আমার স্ত্রী অনায়াসেই বুঝবেন। Retep হচ্ছে পিটার, আমার ছেলে। আর Sbm. Obmota হচ্ছেন Mrs. Mobota আমার পুত্রের গর্ভনেস; কিউবান মহিলা একজন। ছুটি নিয়ে দেশে গেছেন; এ বছর আর ফিরবেন বলে মনে হয় না।
ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল ম্যাককিলভির। অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় হল সে।
ঘটনাটা জানাজানি হয়ে যায়। সিকিউরিটি অফিসার ম্যাককিলভির নাকে ফাইনম্যান ঝামা ঘষে দিয়েছেন–এ খবরে সবাই খুশি। এরপর থেকে অনেকেই ওঁর পরামর্শ নিতে আসে–কেমন করে সেনসরকে এড়িয়ে বাড়িতে কোনো বিশেষ খবর জানানো যায়।
ম্যাককিলভির নাকে ফাইনম্যান কী পরিমাণ ঝামা ঘষেছিলেন তা অবশ্য সঠিক জানতে পারেনি কেউ। ঘটনাটা নিম্নেক্তরূপ–
দিনতিনেক পরে ম্যাককিলভি ডাকে একখানা টাইপ করা চিঠি পায়। ছোট্ট চিঠি। তাতে লেখা ছিল; “প্রিয় ইডিয়ট,
তোমাকে চারটে খবর জানাচ্ছি। এই চিঠিখানা পড়েই ছিঁড়ে ফেল। আর খবর চারটে বেমালুম গিলে ফেল। হজম করে ফেল। জানাজানি হলেই তোমার চাকরি নট। বুঝলে হাঁদারাম?
এক নম্বর খবর :প্রফেসর ফাইনম্যানের পিটার নামে কোনো পুত্রসন্তান নেই।
দুই নম্বর : পিটার একজন রাশান-এজেন্টের ছদ্মনাম।
তিন নম্বর : মিসেস মোবোটো নামে কোনো চাকরানী ওঁর নিউ ইয়র্কের ডেরায় কোনোদিন ছিল না।
চার নম্বর : চিঠিতে অক্ষরগুলো আদৌ উল্টোপাল্টা করে সাজানো ছিল না। ছিল, স্রেফ উল্টো করে সাজানো। Retep উল্টো করলে হয় Peter; কেমন তো? এবার SBMOB MOTA কথাটি উল্টে নিয়ে বুঝবার চেষ্টা করত মূর্খ-সম্রাট-কথাটা জানাজানি হলে তোমার চাকরি থাকবে কিনা!
Guess Who!”
“বলতো কে?”-র নির্দেশ আধাআধি পালন করেছিল ম্যাককিলভি। চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলে; কাউকে জানায়নি, কিন্তু খোঁজ নিয়ে জেনেছিল, ওই অজ্ঞাত পত্রলেখকের প্রথম ও তৃতীয় সংবাদ নিছক সত্য!
এ কাহিনি-বর্ণিত বিশ্বাসঘাতক যতদিন না গ্রেপ্তার হয় ততদিন–দীর্ঘ তিনটি বছর ম্যাককিলভি নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারেনি। তার হিতৈষী ওই পত্ৰলেখককে খুঁজে বার করবার চেষ্টাই করেনি সে। অনুশোচনায় আর অন্তর্দ্বন্দ্বে কাটা হয়ে ছিল। পাক্কা তিনটি বছর।
***
লস অ্যালামসে নীলস বোহর-এর প্রথম আবির্ভাব প্রসঙ্গেও ফাইনম্যানের নামটা লিপিবদ্ধ রয়েছে দেখছি। প্রফেসর বোহর কী একটা নূতন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। লস অ্যালামসের বিজ্ঞানীদের তিনি সেটা জানাবার জন্য এসে হাজির হলেন, লেকচারের নির্ধারিত দিনের আগের দিন। পরদিন প্রফেসর বোহর একটা নূতন কিছু বলবেন, তাই একটা চাঞ্চল্য স্বতই দেখা গিয়েছিল লস অ্যালামসে। সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা ফাইনম্যানের ঘরে টেলিফোনটা হঠাৎ বেজে উঠল। ফাইনম্যান কোনো ধাঁধা কষছিলেন কিনা জানি না, টেলিফোনটা তুলে নিয়ে বলেন, হ্যালো!
–আমি জিম বেকার বলছি। আমরা এইমাত্র এসে পৌঁছেছি। বাবা আপনার সঙ্গে একবার দেখা করতে চান। আপনি একবার গেস্ট-হাউসে আসবেন?
ফাইনম্যান অবাক হয়ে বলেন, জিম বেকার। আমি ঠিক আপনাকে তো–
–আবার বাবার নাম নিকোলাস বেকার!
চমকে উঠেন ফাইনম্যান! মনে পড়ে যায় সব কথা। নীলস্ বোহরের পুত্র অ্যাগী বোহরও যে এসেছে আমেরিকায়, একথা স্মরণ হয়। নিশ্চয়ই তার ছদ্মনাম–জিম।
অবাক হয়ে ফাইনম্যান বলেন, আপনি ভুল করছেন না তো? আমাকে আপনার বাবা কেন খুঁজবেন? আমার নামই জানেন না তিনি।
–জানেন। আপনি মিস্টার হেইলি তো?
–হ্যাঁ, তাই বটে। আচ্ছা আমি এখনই আসছি।
ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে হাজির হলেন গেস্ট-হাউসে। প্রফেসর বোহর ওঁকে দেখেই বললেন, তোমার নামই তো ফাইনম্যান?
-ইয়েস, প্রফেসর।
–ঠিক আছে। বস। এই দেখ আমার রিপোর্ট।
রিপোর্ট দেখবেন কি? ফাইনম্যান তখনও ভাবছেন, লস অ্যালামসে এত এত পণ্ডিত থাকতে হঠাৎ তাকে পাকড়াও করলেন কেন প্রফেসর বোহর। পরদিন যে রিপোর্ট সকলকে পড়ে শোনাবেন, হঠাৎ তা এই ভ্রমণ-ক্লান্ত দিবাশেষে ওঁকে শোনাতে বসলেন কেন বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক? কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যেই বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেল তার। আকণ্ঠ ডুবে গেলেন অঙ্ক-সমুদ্রে। তারপরেই হঠাৎ চীৎকার করে ওঠেন, কী লিখেছেন মশাই পাগলের মতো! এ কী হয়? আটটা ‘আন্-নোন’ আর সাতটা ইকোয়েশন’-এ তো কোনোদিনই সমাধান করা যাবে না।
পাশে দাঁড়িয়েছিল জিম বেকার। কর্ণমূল লাল হয়ে ওঠে তার। কোনো মরমানুষ তার পিতৃদেবকে ‘পাগল’ বলছে এমনটা সে শোনেনি জীবনে। প্রফেসর বোহর কিন্তু নির্বিকার। বলেন, কারেক্ট। কিন্তু এই অষ্টম ইকোয়েশনটাও তো আমাদের হাতে আছে!
শীতালী পাখির মতো ‘ফাই-থিটা-এপসাইলনের একটা ঝাক নেমে এল ব্ল্যাকবোর্ডে।
ফাইনম্যান বলেন, আই সি। আসুন তাহলে কষে ফেলা যাক।
রাত তিনটে নাগাদ শেষ হল অঙ্কটা!
ভোররাত নাগাদ প্রফেসর বোরকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে এলেন উনি ঘর ছেড়ে। জিম বেকার এগিয়ে এল ওঁকে গাড়িতে উঠিয়ে দিতে। গাড়িতে উঠে হঠ। ফাইনম্যান প্রশ্ন করেন, একটা কথা, জিম। তোমার বাবা এত লোক থাকতে আমাকেই বা ডেকে পাঠালেন কেন?
–আপনার কথা বাবা শুনেছিলেন শিকাগো থাকতেই!
–কিন্তু এখানে তো ধুরন্ধর বৈজ্ঞানিক আরও অনেক আছেন–ফের্মি, হান্স বেথে, ৎজিলাৰ্ড, ফন নয়ম্যান…
-জানি। তাদের কেউ আমার বাবাকে ‘পাগল’ বলবার সাহস রাখেন না—
–পাগল! পাগল কে বললে?
–আপনি বলছেন।
–হুঁ! মি? ইম্পসিবল। আমি, ডিক ফাইনম্যান প্রফেসর নীলস বোহরকে..এ সব কী বকছ পাগলের মতো?
–বাবা বলেছিলেন–আর সকলেই তার থিয়োরিটা বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেবেন। তার প্রতি শ্রদ্ধায়, সৌজন্যে, প্রতিবাদ করবেন না-ভুলগুলো তাদের নজরে পড়বে না। পারলে আপনিই–
–তাই বলে আমি প্রফেসর বোহরকে ‘পাগল’ বলব?
–বলব নয় স্যার, বলেছেন। আমি নিজের কানে শুনেছি।
গাড়ি থেকে নেমে আসেন ফাইনম্যান। বলেন, তাহলে চল ক্ষমা চেয়ে আসি।
–প্লিজ প্রফেসর! বাবা শুয়ে পড়েছেন। রাত সাড়ে তিনটে বাজে!
মন ভার করে ফাইনম্যান ফিরে এলেন নিজের ঘরে। না না, এ অসম্ভব। তিনি কখনও বিংশ শতাব্দীর বিস্ময় প্রফেসর নীলস বোহরকে ‘পাগল’ বলতে পারে? তিনি? ডিক ফাইনম্যান! জিম বেকার বৃথাই বকছে পাগলের মতো!
***
ফাইনম্যানের আর এক বাতিক ছিল মুখে মুখে চুটকি কবিতা রচনার। স্রেফ পা-টানা। প্রফেসর নীলস বোহরকে রুদ্ধদ্বার কক্ষে মধ্যরাত্রে যে তিনি ‘পাগল’ বলেছেন এটা জিম বেকার কাউকে বলেনি। পরদিন বোহর বক্তৃতা দিলেন। তার প্রস্থানের পর অন্যান্য সহ-বিজ্ঞানীরা ফাইনম্যানকে বললেন, কেমন লাগল প্রফেসর বোহরকে?
ফাইনম্যান তৎক্ষণাৎ মুখে মুখে জবাব দিলেন :
Professor Bohr প্রফেসর বোহর
Knows no whore! মোর মনচোর!
Drinks no liquor কামিনীকাঞ্চনত্যাগী
Is no bore. সন্ন্যাসী ঘোর!
স্থিতপ্রজ্ঞ ড্যানিশ অধ্যাপকের অনেক জীবনীকার দীর্ঘ রচনায় তার দেবতুল্য চরিত্র সম্বন্ধে লিখে গেছেন, কিন্তু মাত্র চারটি ছত্রে ফাইনম্যান যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছিলেন, তা বোধহয় অনবদ্য। কবিতাটি শুনেই ক্লাউস ফুকস্ বলে ওঠেন : আরে আরে! আপনি করছেন কি, প্রফেসর! বোহর আবার কে? শুনলেন না, ওঁর নাম নিকোলাস বেকার?
ফাইনম্যান বলেন, আই বেগ য়োর পাৰ্ডন। সে ক্ষেত্রে আমি বলব :
Nicholas Baker, নিকোলাস বেকার-যুগান্তকারী।
Epoch-maker. অ্যাটমের শিরে যিনি–হানেন বাড়ি।
Atom-breaker! এহ বাহ্য! তিনি–খাননা তাড়ি!!
Yet he is not A liquor-taker!!
চরমতম অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স! যেন যুগান্তকারী আবিষ্কার করা অথবা পরমাণুর অন্তর বিদীর্ণ করাও কিছু নয়! তার চেয়েও বড় বিস্ময় : লোকটা মদ খায় না।
হো হো করে হেসে ওঠে সবাই। ৎজিলাৰ্ড বলেন : এবার ক্লাউস ফুকস-এর নামে একটা হোক। ওই তোমার ভুলটা ধরিয়ে দিয়েছে।
ফাইনম্যানের জাপানি-তাংকা মুখে মুখে প্রস্তুত :
Fuchs ফুকসহেব তো ধর্মের এক ষণ্ড।
Looks একাই পারেন করতে গাজন পণ্ড।
An ascetic. সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসী এক ভণ্ড।
Theoretic!
অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে সবাই। অর্থাৎ প্রফেসর বোহর হচ্ছেন সত্যিকারের বৈজ্ঞানিক আর ক্লাউস ফুকস্ হচ্ছে ভেকধারী। দেখলে মনে হয় সন্ন্যাসী, আসলে পাজির পা-ঝাড়া।
***
ফাইনম্যানের কীর্তিকাহিনি সবিস্তারে বলতে গেলে আলাদা একখানা বই লিখতে হয়। তবু আরও দু-চারটে কথা বলি। কারণ এই চরিত্রটিকে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেনি কর্নেল প্যাশ–এ কাহিনির গোয়েন্দা। তার বারে বারে মনে হয়েছিল সমস্ত প্রক্রিয়াটা মাইক্রোফিলমে রূপান্তরিত করে রাশিয়ান গুপ্তচরকে হস্তান্তরিত করার হিম্মৎ ছিল ওই ছেলেমানুষিতে-ভরা ফাইনম্যানের!
লস অ্যালামসের ইতিহাসের রচয়িতা ‘মানহাটান প্রজেক্ট’ গ্রন্থে লিখেছেন
“It also afforded Feynman great amusement to work-out the combination numbers of the steel safes in which the most secert and important data of research were kept. In one case he actually succeeded, after weeks of study, in opening the main file-cupboard at the records centre in Los Alamos, while the officer-in-charge of it was absent for a few minutes. Feynmann contented himself, in the brief period during which he had all the atomic secrets at his disposal, with placing in the safe a scrap of paper on which he had written : Guess Who?”
বুঝুন কাণ্ড! কী বলবেন এমন লোককে? খেয়ালী? পাগল? ছেলেমানুষ? না কি ধূর্তস্য ধূর্ত ক্রিমিনাল? যে সিন্দুকে গোপনতম তথ্য রাখা থাকে তা ওই লোকটা কোন্ কায়দায় খুলে ফেলল মাত্র কয়েক মিনিট সুযোগে? আর কেন খুলল? কী উদ্দেশ্য তার? শুধুই সবাইকে চমকে দিতে? ‘বলতো কে?’–লেখা একটা কাগজ ওই আলমারির খোপে রেখে আসবার ছেলেমানুষিতে?
অদ্ভুত প্রতিভা ছিল এই ফাইনম্যানের। প্রফেসর বোহর শিকাগোতে বসে কেমন করে তার নাম জানলেন সেটাও আন্দাজ করতে পারি Grauff-এর লেখা ‘মানহাটান প্রজেক্ট’ গ্রন্থ থেকে। উনি লিখেছেন
“ফাইনম্যানকে শিকাগোতে প্রতিটি গ্রুপের কাজ দেখতে যেতে হত। সেখানে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীরা-কম্পটন, উইগনার, টেলার অথবা ফের্মি তাকে নানা উপদেশ দিতেন। একবার হঠাৎ ওঁর কানে গেল–কী একটা অঙ্ক শিকাগো-গ্রুপ দীর্ঘদিন ধরে কষতে পারছেন না। কৌতূহলী ফাইনম্যান জানতে চাইলেন, অঙ্কটা কী? শুনে, মাত্র আধঘণ্টার মধ্যে সেটা কষে দিলেন তিনি। ফিরে এসে উনি ওর বন্ধুকে বলেছিলেন–বড়কর্তারা আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছেন তো, তাই একটু গুরুদক্ষিণা দিয়ে এলাম।”
খবরটা জানতে পেরেছিলেন নীলস বোহর।
আর একবার। গভর্নিং বোর্ডের মিটিংয়ে একজন বৈজ্ঞানিক বললেন, IBM কোম্পানি একরকম নতুন কম্পুটার-বার করেছে যাতে অত্যন্ত দ্রুত যান্ত্রিক পদ্ধতিতে অঙ্ক কষা যায়। কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে নাকি এগুলি বসানো হয়েছে। অনেক আলোচনার পর ওই যন্ত্র কেনা ঠিক হল। তখনও ইলেকট্রনিক কম্পুটার চালু হয়নি কোথাও। অর্ডার গেল আই. বি. এম. কোম্পানির কাছে। যন্ত্রটা নতুন, তার ব্যবহার কেউ জানে না–তাই কোম্পানিকে লেখা হল যারা যন্ত্রটা বসাতে আসবে তাদের সঙ্গে যেন মেশিনম্যানও পাঠানো হয়। মানহাটান প্রকল্পে তারা থেকে যাবে। যন্ত্রগুলো চালাবে।
যা হয়। কোম্পানি পত্রপাঠ যন্ত্রগুলো পাঠিয়ে দিল। তারপর শুরু করল চিঠি-চাপাটি। যারা মেশিন চালাবে তাদের কী হারে মাইনে দেওয়া হবে, তাদের চাকরির নিরাপত্তা কতদূর, থাকবার কী ব্যবস্থা হবে ইত্যাদি। বড় বড় প্যাকিং কেস পড়ে রইল গুদামে আর কোম্পানি শুরু করল দরকষাকষি! যাই হোক, দিন পনেরো পর এল কোম্পানির লোক–কিন্তু কোথায় গেল সেই প্যাকিং কেসগুলো? সেগুলো তো গুদামে নেই। ফাইনম্যান হচ্ছেন বিভাগীয় কর্তা। বড়কর্তা তাকে প্রশ্ন করেন, সেই প্রকাণ্ড প্যাকিং কেসগুলো কোন্ গুদামে আছে? লোক এসে গেছে যে! ফাইনম্যান বলেন, কোগুলো স্যার? সেই আই. বি. এম. কম্পুটারগুলো? লোক আসতে দেরি হচ্ছিল দেখে আমি নিজেই যন্ত্রটা বসিয়ে নিয়েছি। হ্যাঁ, খুব ভালো যন্ত্র। ব্যবহার করছি তো আজ দিন সাতেক। চমৎকার জিনিস!
কোম্পানির লোক এবং ডিরেক্টার স্তম্ভিত। স্বচক্ষে দেখতে এলেন তারা। হ্যাঁ, কাজ হচ্ছে। পুরোদমে কাজ হচ্ছে মেশিনে!
বিস্মিত হয়ে ডিরেক্টার বলেন, কী আশ্চর্য! এ যন্ত্রটা তো সদ্য-আবিষ্কৃত। কেমন করে বসালে হে! এমন কমপ্লিকেটেড ইলেকট্রনিক কম্পুটার।
–ছেলেবেলায় আমি যে মেকানো বানাতাম স্যার-ফাইনম্যানের সাফ জবাব।
-তাই বলে এত লক্ষ ডলার দামের যন্ত্র কাউকে কিছু না বলে তুমি খুলে ফেললে?
–কী যে বলেন স্যার ‘পাগলের মতো’! সাতদিন এগিয়ে গেল না আমাদের কাজ?
কোম্পানি-প্রেরিত লোকগুলো অবশ্য চাকরি পেল। দিন দশেক পরে মসকুইটো বোট আবার এসে হানা দিলেন ব্যাটলশিপের ঘরে। বললেন, ওই লোকগুলো কাজে উৎসাহ পাচ্ছে না। দৈনিক আটঘণ্টা ডিউটি দিচ্ছে–কিন্তু কাজে প্রাণ নেই যেন।
-কেন প্রাণ নেই?
-কেমন করে থাকবে? কিসের অঙ্ক কষছে তাই যে ওরা জানে না! ওদের বলে দেওয়া উচিত ওরা কিজন্য এই মেশিন চালাচ্ছে। তাহলেই ও বা উৎসাহ পাবে।
ফাইনম্যানের বাঁধা-লবজটাই বলে বসলেন ডিরেক্টার-পাগলের মতো কথা বলো না! ওদের ওসব কথা জানানোর আইন নেই!
—আমি ডক্টর ওপেনহাইমারকে বলে দেখব?
–দেখতে পায়। সে রাজি হবে না।
কিন্তু ফাইনম্যান নাছোড়বান্দা; পাগলটাকে রোখা যাবে না জেনে শেষ পর্ষ ওপেনহাইমার রাজি হলেন। ফাইনম্যান ওই মেশিনম্যান ছোকরাদের ব্যাপারট। একদিন ভালো করে বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, তোমরা আসলে তৈরি করছ অ্যাটম-বোমা। তোমরা তার এক-একটা নাট বল্ট! বুঝলে?
আশ্চর্য! সাতদিনের মাথায় ফাইনম্যান এসে দাখিল করলেন তার পরিসংখ্যান। মেশিনের আউটপুট হান্ড্রেড-পার্সেন্ট বেড়ে গেছে। বলেন, দেখলেন স্যার? আপনারা শুধু আপত্তিই করছিলেন পাগলের মতো।
.
০৯.
‘কাগুজে-বাঘ’ কথাটা আজকাল প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। আমার তো মনে হয়েছে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় কাগুজে-বাঘ হচ্ছে জার্মান অ্যাটম-বোমা! এই বাঘের ভয়েই একদিন রুজভেল্ট বলেছিলেন, ‘পা। এটার ব্যবস্থা হওয়া দরকার। এই বাঘের ভয়ে কোটি কোটি ডলার ব্যয়ে মার্কিন-সরকার মানহাটান-প্রকল্পে হাত দিয়েছেন। জার্মান-বৈজ্ঞানিকদের আগেই আমেরিকায় অ্যাটম-বোমা তৈরি করে ফেলতে হবে।
যুদ্ধের শেষাশেষি এক গবেষকদল জার্মানিতে গিয়ে অনুসন্ধান করে দেখেছিলেন, জার্মানিতে পরমাণু-বোমা সম্বন্ধে কতদূর কী করা হয়েছিল। সে অনুসন্ধানের ফলশ্রুতি–জার্মান-বৈজ্ঞানিকরা অ্যাটম-বোমা থেকে অনেক অনেক দূরে ছিলেন। এটা প্রথমটা অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল। অটো হান, হেইসেনবের্গ, ওয়াইৎসেকার বা ফন লে-র মতো অসীম প্রতিভাধরদের এ অসাফল্যের কারণ কী? সে কথাই বলব এবার।
জার্মান যুদ্ধের একেবারে শেষ পর্যায়ে একটি মার্কিন মিশন এল যুদ্ধবিধ্বস্ত জার্মানিতে–এল গবেষণা করে দেখতে, জার্মানি অ্যাটম-বোমা বানানোর চেষ্টায় কতদূর কী করতে পেরেছিল। তার একটা বিশেষ কারণও ছিল। 1942-এর ডিসেম্বরে মার্কিন গুপ্তচর-বাহিনী খবর পেল বড়দিনের দিন হিটলারের বিমানবহর অতলান্তিক পাড়ি দিয়ে নাকি মার্কিন ভূখণ্ডে বোমাবর্ষণ করতে আসছে। সাধারণ বোমা নয়, পরমাণু বোমা। ওদের লক্ষ্যস্থল নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন অথবা শিকাগো। খবরটা এমন আতঙ্ক ছড়িয়ে ছিল যে, বড়কর্তারা নানান অজুহাতে স্ত্রী-পুত্র পরিবারকে বড়দিনের আনন্দ উৎসব থেকে বঞ্চিত করে গ্রামাঞ্চলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বড়দিন পার হয়ে গেলো। বোমা পড়ল না। পরের বছর জানুয়ারিতে তৈরি করা হয় এই মিশন অ্যালসস্। তার কর্ণধার কর্নেল প্যাশ। যাঁকে এ কাহিনির প্রথম অধ্যায়ে আমরা চিনেছি।
কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারলেন প্যাশ-এর মতো ‘অ-পদার্থ-বিদ’কে দিয়ে কাজ হবে না। তাই ওঁরা খোঁজ করতে শুরু করেন এমন একজনকে যিনি পদার্থবিদ্যাতে পারদর্শী এবং অপরাধ-বিজ্ঞানেও। পাওয়া গেল তেমন সব্যসাচী। স্যামুয়েল গাউডসমিট। ওলন্দাজ বৈজ্ঞানিক। গোটিনজেন-এর প্রাক্তন-ছাত্র– হেইসেনবের্গের সহাধ্যায়ী অথচ ক্রিমিনোলজি হচ্ছে তার প্যাশন। বৃদ্ধ বাবা-মা হল্যান্ডেই আছেন। যুদ্ধের আগেই উনি ডেনমার্কে পালিয়ে যান, প্রফেসর বোহর-এর অধীনে ডক্টরেট লাভ করে পাড়ি জমান মার্কিন মুলুকে। বর্তমানে ম্যাসাচুটেস-এ রেডার-প্রকল্পে নিযুক্ত।
মনের মতো কাজ পেলেন গাউডসমিট। প্রথমত, গোয়েন্দা কাহিনির নায়ক হলেন; দু-নম্বর, বৃদ্ধ পিতামাতার সঙ্গে সাক্ষাতের একটা সম্ভাবনা দেখা দিল। গত তিন বছর তাদের কোনো চিঠিপত্র পাননি। হল্যান্ড এতদিন ছিল নাৎসিবাহিনীর দখলে!
গাউডসমিট-এর এই অনুসন্ধানকার্য আর একটা পৃথক গোয়েন্দা বিষয়বস্তু হতে পারে। স্থানাভাবে আমাকে দু-একটা ইঙ্গিত দিয়েই শেষ করতে হল। কৌতূহলী পাঠক গাউডসমিট-এর স্মৃতিচারণ Alsos’ পড়ে দেখতে পারেন।
তার গ্রন্থ পড়ে জানতে পারছি, নোবেল-লরিয়েট বৈজ্ঞানিক জোলিও-কুরি অধিকৃত-পারিতে বন্দুক হাতে রাস্তার লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন! বর্ণনা দিয়েছেন–কীভাবে ফরাসি পদার্থবিদ জর্জেস ব্রুহাট মৃত্যুবরণ করেন। প্রফেসর ব্রুহাট-এর ছাত্র রাউসেল পারির মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। গেস্টাপো অপরিসীম যন্ত্রণা দিয়েও প্রফেসার ব্রুহাট-এর কাছ থেকে তার ছাত্রের ঠিকানা জানতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত তারা বৃদ্ধ প্রফেসরকে পাঠিয়ে দেয় একটা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে। অধ্যাপক নির্বিচারে মেনে নিলেন এই বন্দীজীবন। সেখানে তিনি বন্দীদের নিয়ে গণিত-জ্যোতিষ চর্চা করতেন–আকাশের তারা চেনাতেন। অনাহারে শেষ পর্যন্ত প্রফেসর ব্রুহাট মারা যান।
বলেছেন, হলওয়েক-এর কথাও। হলওয়েক একটা নতুন ধরনের মেশিনগান আবিষ্কার করে উপহার দিয়েছিলেন পারির মুক্তি ফৌজকে। এ কথা জানতে পেরেছিল গেস্টাপো। হলওয়েক ধরা পরার পর জার্মান গুপ্তচরেরা বৈজ্ঞানিককে ওই আবিষ্কারের সূত্রটা তাদের জানিয়ে দেবার জন্য নিপীড়ন শুরু করে। তিল তিল করে মৃত্যু বরণ করেছিলেন হলওয়েক–তার অতিপ্রিয় মুক্তি ফৌজের বিরুদ্ধে তার আবিষ্কারকে ব্যবহৃত হতে দেননি।
***
গাউডসমিট-এর তালিকায় ছিল চারটি নাম। চারজনের পক্ষেই পরমাণু-বোমার হৃদয় বিদীর্ণ করা সম্ভব। তারা হচ্ছেন–অটো হান, ফন লে, ওয়াইৎসেকার আর হেইসেনবের্গ। বিধ্বস্ত জার্মানির এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে তিনি খুঁজে ফিরেছেন ওই চারজনকে। খবর পেয়েছিলেন, স্ট্রাসবের্গ-এ ছিল ওঁদের মূল কেন্দ্র। স্ট্রাসবের্গ তখনও নাৎসি ফৌজের দখলে। অবশেষে 1944-এ পনেরই নভেম্বর জেনারেল প্যাটন-এর বিজয়ী বাহিনী প্রবেশ করল স্ট্রাসবের্গ-এ। কর্নেল প্যাশ একটি সাঁজোয়া গাড়িতে গাউডসমিটকে নিয়ে মেশিনগানের গুলিবর্ষণের ভিতরেই প্রবেশ করলেন স্ট্রাসবের্গে। গবেষণাগারের অবস্থান দেখানো ম্যাপ সঙ্গে ছিল। খুঁজে পেতে দেরি হল না। সৈন্যদের নিয়ে ওঁরা ঢুকে পড়লেন ল্যাবরেটারির ধ্বংসস্তূপে। না, চারজনের একজনেরও সন্ধান পেলেন না। তবে যারা বন্দী হলেন তাদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি পাওয়া গেল–কিছুদিন আগেও ওঁরা এখানে ছিলেন। শহরের পতন আসন্ন বুঝতে পেরে জার্মান-বিজ্ঞানের চার মধ্যমণি পালিয়েছেন কাইজার উইলহেম ইন্সটিটুটে। বিজ্ঞানীদের ধরা গেল না, উদ্ধার করা গেল কিছু গোপন নথি। সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা।
ক্রিমিনোলজি ছিল গাউডসমিটের বিলাস। সারারাত মোমবাতির আলোয় গবেষণা করে তিনি ওই সাঙ্কেতিক-ভাষা ডি-কোড করলেন। পাঠোদ্ধারের পর বোঝা গেল রিপোর্টটা তৈরি করছেন স্বয়ং ওয়াইৎসেকার, স্বহস্তে। মাত্র দু-মাস পূর্বের রচনা। তা থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা গেল, জার্মান-বৈজ্ঞানিকেরা ইউরেনিয়াম অথবা প্লুটোনিয়ামের পরমাণুকে ক্রমাগত বিদীর্ণ করতে তখনও কোনো ‘চেইন-রিয়্যাকশন’ বার করতে পারেননি। ইউ-238 থেকে ইউ 235-এর বিচ্ছিন্নকরণও সম্ভব হয়নি। তৎক্ষণাৎ বিস্তারিত রিপোর্ট লিখে ডক্টর গাউডসমিট পাঠিয়ে দিলেন আমেরিকায়। স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল তার।
মার্কিন কর্তৃপক্ষ কিন্তু এ তথ্য আদৌ বিশ্বাস করতে পারলেন না। জবাবে তারা জানালেন, “আমাদের সন্দেহ, সহজে ভাঙা যায় এমন সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখে ওয়াইৎসেকার ইচ্ছা করেই ওই রিপোর্ট ল্যাবরেটারিতে রেখে গেছেন, আমাদের চোখে ধুলো দিতে। দ্বিতীয় কথা, আপনার ধারণা ভ্রান্তও হতে পারে। অটো হান, ফন লে, ওয়াইৎসেকার অথবা হাইসেনবের্গ ছাড়াও অখ্যাত অজ্ঞাত কোনো বৈজ্ঞানিক হয়তো নির্জন সাধনায় ওই আবিষ্কার করে বসেছেন, যার কথা আপনি কল্পনাও করতে পারছেন না।”
এ-কথার জবাবে ওই মিলিটারি বড়কর্তাকে অভিমানী নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট যে-কথা লিখেছিলেন তার আর অনুবাদ হয় না! যুদ্ধকালে সামরিক কর্তা এবং ডিপ্লোম্যাটেরা বরাবরই বৈজ্ঞানিকদের ওপর ছড়ি ঘুরিয়েছেন। প্রফেসর বোহর, ম্যাক্স বর্ন অথবা জেমস ফ্রাঙ্কের মতো বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিকদের নির্বিচারে আদেশ পালন করতে বাধ্য করেছেন ওই সব সামরিক কর্তা আর রাজনীতির পণ্ডিতম্মন্যের দল। গাউডসমিট-এর এই চাবুকের মতো জবাবটি যেন সেই অপমানের প্রতিশোধ! গাউডসমিট মার্কিন সমরনায়ককে লিখেছিলেন :
“A paper-hanger may perhaps imagine that he has turned into a military genius overnight, and a trader in champagne may be able to disguise himself as a diplomat. But laymen of that sort could never have acquired sufficient scientific knowledge, in so short a time, to be able to construct an atom bomb.
[কোনো রংমিস্ত্রি হয়তো মনে করতে পারে রাতারাতি সে একজন সামরিক ধুরন্ধর হয়ে উঠেছে অথবা কোনো ভাঁটিখানার শুঁড়ি রাত-পোহালে বিখ্যাত রাজনীতিকের ছদ্মবেশ হয়তো ধারণ করতে পারে–কিন্তু একজন রাস্তার লোক এত অল্পসময়ে এতটা বৈজ্ঞানিক-জ্ঞান লাভ কিছুতেই করতে পারে না যাতে সে পরমাণু-বোমার নির্মাতা হয়ে পড়বে।]
দুঃখের বিষয় পত্রের প্রাপকটি সামরিক জীবনের পূর্বাশ্রমে রঙের-মিস্ত্রি অথবা মদের কারবারী ছিলেন কিনা এ তথ্যটার সন্ধান পাইনি।
***
আরও পরে মিত্রপক্ষের বিজয়ী বাহিনী অধিকার করল কাইজার উইলহেম ইন্সটিটুট। এবারও সৈন্যদলের সঙ্গে ছিলেন কর্নেল প্যাশ এবং গাউডসমিট! একজন সংবাদবহ এসে খবর দিল, ইন্সটিটুটের ল্যাবরেটারিতে কয়েকজন বৈজ্ঞানিককে তারা গ্রেপ্তার করেছে–চিনতে পারছে না। গাউডসমিট তৎক্ষণাৎ উঠে পড়েন। বলেন, চল এখনই গিয়ে দেখব।
গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এলেন কর্নেল প্যাশ নিজে। প্রশ্ন করেন তিনি, ডক্টর, এবার যদি জালে আপনার প্রাইজ গেম ধরা পড়ে থাকে তবে আপনি তাদের চিনতে পারবেন তো?
ম্লান হাসলেন ডক্টর গাউডসমিট। বলেন, কর্নেল, ওঁদের মধ্যে কেউ আমার অধ্যাপক, কেউ আমার সহপাঠী! আমি চিনব না?
চিনতে কোনো অসুবিধা হল না সত্যই। বন্দী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন যাঁরা, তাঁরা জার্মানির শ্রেষ্ঠ মনীষা–নোবেল লরিয়েট অটো হান, ফন লে এবং ওয়াইৎসেকার সমেত আরও পাঁচজন প্রধান নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট।
-হাউ ডু য়ু ডু প্রফেসর?–প্রশ্ন করেন গাউডসমিট লজ্জায় লাল হয়ে।
-য়ু নিডন্ট ব্লাশ, মাই বয়!-জবাব দিলেন বৃদ্ধ অটো হান। ইউরেনিয়াম পরমাণুর হৃদয় যিনি সর্বপ্রথম বিদীর্ণ করেছিলেন।
ধরা পড়লেন না শুধু হেইসেনবের্গ। রাত তিনটের সময় একটা সাইকেলে চেপে কাইজার ইন্সটিটুট ছেড়ে তিনি নাকি উত্তর ব্যাভেরিয়ার দিকে রওনা হয়ে গেছেন। সেখানে ছিলেন হেইসেনবের্গের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার। শেষ মুহূর্ত কয়টি তিনি তাদের সঙ্গে কাটাতে চেয়েছিলেন। পঁচিশ বছর বয়েসে যিনি নোবেল-প্রাইজ পাওয়ার মতো আবিষ্কার করতে পারেন, কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার পদ প্রত্যাখ্যান করে পরাজয়ের হলাহল আকণ্ঠ পান করে নীলকণ্ঠ হতে যাঁরা কুণ্ঠা নেই, সেই হেইসেনবের্গ রাতারাতি প্রায় একশ কিলোমিটার সাইকেলে পাড়ি দিয়ে চলে গেছেন উত্তর ব্যাভেরিয়ায়।
হেইসেনবের্গ সেইখানেই গ্রেপ্তার হন–আরও পরে।
সেদিন কিন্তু ওঁরা হেইসেনবের্গের সাক্ষাৎ পাননি। তার ল্যাবরেটারির চিহ্নিত ঘরটি তন্নতন্ন করে খোঁজা হল। এখানে একটি জিনিস উদ্ধার করেছিলেন কর্নেল প্যাশ–একটি ফটো! ঘরের টেবিলে ফটো-স্ট্যান্ডে রাখা ছিল। দুটি যুবক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে–কনভোকেশন গাউন পরে। সদ্য ডক্টরেট হয়েছেন তারা। একজন ওয়ার্নার হেইসেনবের্গ আর একজন স্যামুয়েল গাউডসমিট। পলাতক ও পশ্চাদ্ধাবনকারী।
গাউডসমিটের অনুসন্ধানকার্যের মর্মান্তিক উপসংহারের প্রসঙ্গে এবার আসি। খুঁজতে খুঁজতে এবং ঘুরতে ঘুরতে গাউডসমিট এসে পৌঁছলেন হল্যান্ডে-দ্য হেগে। হেগ-এর ন্যাশনাল ইন্সটিটুটে অনুসন্ধান শেষ করে গাউডসমিট তার সহকারীকে বললেন, কর্নেল, একবেলার জন্য ছুটি চাইছি। ওবেলা আমি আসব না।
-কেন? কী করবেন ওবেলায়?
–দ্য হেগ হচ্ছে আমার পিতৃভূমি। শহরের ওপ্রান্তে ছিল আমাদের বাড়িটা। তিন বছর আগেও সেখান থেকে বাবা-মায়ের চিঠি পেয়েছি। বাবার সত্তরতম জন্মদিনে একটা কেও করেছিলাম। জানি না, সেটা পেয়েছিলেন কিনা।
–আয়াম সরি। যান, গিয়ে খোঁজ করে দেখুন।
পনেরো বছর পরে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরছে। রীতিমতো কৃতী সন্তান–বংশের গৌরব। বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল উনিশ বছর বয়সে-জার্মানি, ডেনমার্ক, ইংল্যান্ড ঘুরে পোঁচেছে আমেরিকায়। সদ্য স্কুল থেকে পাশ ছেলে আজ ডক্টরেট পাওয়া প্রৌঢ়। যুদ্ধ বাধার আগে গাউডসমিট আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন বুড়ো-বুড়ির ইমিগ্রেশান পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে মার্কিন মুলুকে নিয়ে যাওয়ার। নানান বাধা বিপত্তিতে সেটা শেষ পর্যন্ত ঘটে উঠেনি। গত তিন বছর কোনো খবরই পাননি।
গাউডসমিটের এই প্রত্যাবর্তনের কাহিনিটা আমি নিজের ভাষায় বলব না; তার রচনার অনুবাদ করে যাব। ভাবানুবাদ নয়, তাতে আমার ভাবালুতা হয়তো অজান্তে মিশে যাবে–আক্ষরিক অনুবাদ :
“জিপটাকে আমাদের বাড়ি থেকে কিছু দূরে রেখে হেঁটেই এগিয়ে গেলাম। বাড়িটা তখনও খাড়া আছে, কিন্তু কাছে এসে দেখলাম, সব কটা জানলাই অদৃশ্য। দরজা বন্ধ ছিল। জানলা দিয়ে লাফ মেরে ভিতরে ঢুকলাম। জনমানব নেই।…এ ঘরটা ছেলেবেলায় ছিল আমার নার্সারি; পরে পড়ার ঘর। চারিদিকে কাগজপত্র ছড়ানো–তার মধ্যে আমার স্কুল-ছাড়ার সার্টিফিকেটখানি। চকিতে মনে পড়ল, এটা বরাবর বাবার ড্রয়ারে সযত্নে রাখা থাকত। দু-চোখ বুজে আমি বিশ-ত্রিশ বছর পিছিয়ে গেলাম। ওইখানে ছিল আমার অন্ধ মায়ের টেবিলটা; এইখানে আমার বুককেসটা। আমার সেই অত অত বই সব কোথায় গেল?…পিছনে মায়ের সখের বাগানটা আগাছায় ভরে গেছে। শুধু লাইলাক গাছটা নীরবে সাক্ষীর মতো দাঁড়িয়ে আছে। সেই ভগ্নস্তূপের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনে হল আমি চরম অপরাধ করেছি।…হয়তো ওঁদের আমি বাঁচাতে পারতাম। আমেরিকান ভিসা পর্যন্ত তৈরি করা হয়েছিল–বাবার এবং মায়ের; যদি আর একটু বেশি ছুটোছুটি করতাম, যদি ইমিগ্রেশন অফিসে আরও বেশি করে ধর্না দিতাম, নিশ্চয়ই ওই নৃশংস নাৎসিদের হাত থেকে ওঁদের আমি রক্ষা করতে পারতাম। কী হয়েছিল তাদের? এখানেই মারা গেছেন? পাড়ার লোক কিছু বলতে পারবে? কিন্তু গোটা পাড়াটাই যে ফাঁকা। চেনা মুখ একটাও দেখছি না…”।
এর মাসখানেক পরে একটি কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে অনুসন্ধান করবার সময় ওই প্রশ্নটির সমাধান হঠাৎ উনি খুঁজে পেয়েছিলেন। গ্যাস-চেম্বারে যাদের পাঠানো হচ্ছে তাদের নাম-ধাম লেখা থাকত একটা রেজিস্টারে। তাতেই উদ্ধার করলেন দুটি নাম। বাবার এবং অন্ধ মায়ের।
গাউডসমিট লিখছেন–
“And that is why, I know the precise date my father and blind mother were put to death in the gas chamber. It was my father’s seventieth birthday”.
“তাই আমি জানি, ঠিক কোনদিন আমার বাবা এবং অন্ধ মা গ্যাস চেম্বারে শেষ দূষিত নিশ্বাস নেন। তারিখটা ছিল আমার বাবার সত্তরতম জন্মদিন।”
***
জার্মানিতে অ্যাটম-বোমা সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত না হওয়ার চারটি প্রধান হেতু। তার প্রথম তিনটির ওপরেই বেশি জোর দিয়েছেন মার্কিন আর ইংরেজ সাংবাদিক এবং ঐতিহাসিকের দল। কিন্তু D. Irving-এর লেখা “The German Atomic Bomb–the History of Nuclear Research in Nazi Germany” szlo পড়ে আমার মনে হয়েছে প্রথম এবং চতুর্থ কারণটাই সর্বপ্রধান।
চারটি হেতু নিম্নোক্তরূপ–
প্রথমত-অনার্য এবং ইহুদি, এই অজুহাতে হিটলার নেতৃস্থানীয় পদার্থবিজ্ঞানীদের বিতাড়ন করেছিলেন। দ্বিতীয়ত–যাঁরা অবশিষ্ট ছিলেন তাঁদের নাৎসি যুদ্ধবাজদের অধীনে এমন দৈহিক ও মানসিক অবস্থার মধ্যে রাখা হয়েছিল যা গবেষণার পরিপন্থী। তৃতীয়ত-যন্ত্রপাতি বা গবেষণার জন্য উপযুক্ত অর্থের ব্যবস্থা করা হয়নি এবং চতুর্থত-বৈজ্ঞানিকদের সাফল্যের বিষয়ে অনীহা, এমনকি অনিচ্ছা!
শেষ যুক্তিটারই বিস্তার করব বিশেষভাবে।
1939-এর ছাব্বিশে সেপ্টেম্বর-অর্থাৎ আলেকজান্ডার সাস্ যেদিন আইনস্টাইনের চিঠি নিয়ে রুজভেল্টের সঙ্গে দেখা করেন তার পনেরো দিন আগে– বার্লিনে জন্ম নেয় ইউরেনিয়াম প্রজেক্ট। নয়জন পদার্থবিজ্ঞানী এতে অংশ নেন–তার ভিতর উপস্থিত ছিলেন না অটো হান, ফন লে, ওয়াইৎসেকার বা হেইসেনবের্গ। এঁরা কেউ আমন্ত্রিত হননি। ওই নয়জনও উঁচুদরের পদার্থ বিজ্ঞানী–কিন্তু তাদের নির্বাচনের আসল হেতু নাৎসিবাদের প্রতি তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন। মাসখানেকের ভিতরেই বোধহয় কর্তৃপক্ষের টনক নড়ল–ডাক পড়ল ওয়াইৎসেকার এবং হেইসেনবের্গের। প্রকল্পের কর্ণধার হলেন দুবাই, তার অধীনে রইলেন হেইসেনবের্গ, যদিও পাণ্ডিত্যে হেইসেনবের্গ-এর স্থান অনেক উচ্চে। অটো হানকেও ডাকা হয়েছিল পরে–কিন্তু হান সর্বসমক্ষে বলে ওঠেন, ‘হিটলারের হাতে অ্যাটম-বোমা তুলে দেওয়ার আগে আমি আত্মহত্যা করব।’
ওঁর এক ছাত্র সৌজন্যের বালাই না মেনে ছুটে এসে মুখ চেপে ধরেছিল শ্রদ্ধেয় অধ্যাপকের।
মোট কথা, দ্বিতীয় শ্রেণির বৈজ্ঞানিকদলের অধীনে শেষ পর্যন্ত ওই চারজনকেই গবেষণার কাজে নিযুক্ত হতে হল। প্রথমে ওঁরা স্থির করেছিলেন প্রতিবাদ করে শহীদ হবেন; কিন্তু মূলত হেইসেনবের্গের বুদ্ধিতেই ওঁরা অন্য পথ ধরেন। ওঁরা ভাব দেখান যেন আপ্রাণ প্রচেষ্টাতেও কিছু করতে পারছেন না। এই প্রসঙ্গে স্বয়ং হেইসেনবের্গ যুদ্ধান্তে এক বিবৃতিতে বলেছিলেন–
“ডিক্টেটারশিপে তারাই সক্রিয়ভাবে বাধার সৃষ্টি করতে পারে, যারা ভান করে যায় শাসনযন্ত্রের সঙ্গে সবরকম সহযোগিতা করতে তারা প্রস্তুত। প্রতিবাদের অর্থ বন্দীশিবিরে আবদ্ধ হওয়া। সেখানে শহীদ হয়েও লাভ নেই–কেউ তার নাম বা মতাদর্শের কথা জানতে পারবে না। তার নামোচ্চারণই নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। বিশে জুলাই যারা নাৎসিবাদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করে প্রাণ দিল–তাদের মধ্যে আমার কিছু বন্ধুও আছে–তাদের কথা মনে করে আমার আত্মানুশোচনা হয়। আবার ভাবি–ওরাই কি প্রমাণ করে দিয়ে গেল না, ওই শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার–তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার, একমাত্র পথ হচ্ছে সহযোগিতার ভান করে যাওয়া?”
এর পর জার্মান বৈজ্ঞানিকের দল পরমাণু বোমা বানানোর প্রতিযোগিতায় কেন ব্যর্থ হয়েছিলেন সেকথা বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে না।
***
আর একটি ঘটনার উল্লেখ করে এ পরিচ্ছেদের যবনিকা টানব। যুদ্ধ চলাকালে হাইসেনবের্গের সঙ্গে প্রফেসর নীলস বোহর-এর সাক্ষাৎ। তখনও প্রফেসর বোহর ডেনমার্ক ছেড়ে পালিয়ে আসেননি। ডেনমার্ক তখন নাৎসি অধিকারে। বোহর তার ইহুদি এবং অনার্য সহকারী বন্ধুদের সকলেই ইংল্যান্ড বা আমেরিকায় পাচার করেছেন–শূন্য ল্যাবরেটরি আঁকড়ে তিনি একা পড়ে আছেন শুধু এই বিশ্বাসটুকু নিয়ে যে, হিটলার অন্তত তাকে কনসেনট্রেশান ক্যাম্পে পাঠাবে না। ভয়ে সবাই কাটা হয়ে আছে।
এই সময় অটো হান, হেইসেনবের্গ প্রভৃতি স্থির করলেন প্রফেসর বোহর-এর সঙ্গে যোগাযোগ করা নিতান্ত প্রয়োজন। আমেরিকা যেমন জার্মান পরমাণু-বোমার ভয়ে ভীত–এইসব বৈজ্ঞানিকও অনুরূপভাবে ভাবছিলেন, মার্কিন পরমাণু-বোমায় তাদের সাধের জার্মানি ধ্বংসপুরীতে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে। তাদের দুঃখটা আরও বেশি–কারণ অতলান্তিকের ওপারে যারা বোমা বানাচ্ছেন, তাঁরা অনেকেই জার্মান-ফ্রাঙ্ক, ম্যাক্স বর্ন, ৎজিলাৰ্ড, ফুস্, হান্স বেথে–সবাই ওঁদের ঘরের লোক। ওইসব মার্কিন-প্রবাসী মধ্যযুরোপিয়দের একটা খবর দেওয়া দরকার যে, জার্মান পরমাণু-বোমা একটি কাগুজে-বাঘ। তার ভয়ে আগেভাগেই তোমরা এ-দেশটাকে শ্মশানে পরিণত করো না। এ খবর পশ্চিমখণ্ডে পৌঁছে দেওয়ার মতো উপযুক্ত লোক একমাত্র ডেনিশ বৈজ্ঞানিক নীলস বোহর। তার কথা এমন কেউ অবিশ্বাস করবে না যে ফিজিক্স বইয়ের প্রথম পাতাটা উল্টেছে। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘন্টাটা কে বাঁধে? ওঁরা এই দৌত্যকার্যে পাঠালেন স্বয়ং হেইসেনবের্গকে। হেইসেনবের্গ ‘ইউরেনিয়াম-প্রকল্পের ডেপুটি ডাইরেকটার, তার একটা পদমর্যাদা আছে। তার চেয়েও বড় কথা, হেইসেনবের্গ হচ্ছেন নী বোহরের অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র।
গুরুশিষ্যের সাক্ষাৎকারটা নিতান্তই দুর্ভাগ্যজনক!
তার একটা কাকতালীয় হেতু আছে। হেইসেনবের্গ তার থিয়োরি অনুসারে দু-নৌকায় পা দিয়ে চলছিলেন। বাহ্যত জার্মান-সরকারকে মদত দিতে হচ্ছিল তাঁকে, যাতে তার সহকর্মী বৈজ্ঞানিকদের ওপর নাৎসি অত্যাচার না হয়। এজন্য জার্মানি যখন পোলান্ড অভিযান করে তখন এক সম্বর্ধনা সভায় হেইসেনবের্গ। হিটলারকে প্রশংসা করে একটি বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। ঘটনাচক্রে সেটা নজরে পড়েছিল তার অধ্যাপক নীলস বোহর-এর। তাই বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিকের ধারণা হয়েছিল তার প্রিয় ছাত্র হেইসেনবের্গ নাৎসি শাসকদের অন্ধ ভক্ত। ওই ‘বাইরে-এক ভিতরে-আর’ নীতি কল্পনাই করতে পারেন না সহজ সরল সোজাপথের পথিক নীলস বোহর। তাই হেইসেনবের্গ যখন কোপেনহেগেন-এ এসে তার অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করলেন তখন অত্যন্ত গম্ভীর এবং উদাসীনভাবে তাকে গ্রহণ করলেন প্রফেসর বোহর। অনেকক্ষণ কথা বলেছিলেন দু-জনে, জনান্তিকেই কিন্তু কেউই মন খুলে প্রাণের কথা বলতে পারেননি। দুজনেই দুজনকে ভয় পাচ্ছিলেন। হেইসেনবের্গ শেষ পর্যন্ত মরিয়া হয়ে প্রশ্ন করে বসলেন, আপনি কি মনে করেন অনতিবিলম্বে পরমাণু-বোমা তৈরি হতে পারে?
নীলস বোহর জবাবে বলেছিলেন, আমি তা মনে করি না।
–কিন্তু আমি করি স্যার। আমার দৃঢ় ধারণা, চেষ্টা করলে আমরা অনতিবিলম্বে ওই রকম বোমা তৈরি করতে পারি।
উদাসীনভাবে বোহর বলেন, হতে পারে। নাৎসি জার্মানির ভিতরে তোমরা কতদূর কী করেছ তা জানব কেমন করে?
হিতে বিপরীত হচ্ছে বুঝতে পেরে হেইসেনবের্গ বলেন, সে-কথা বলছি না। স্যার। আচ্ছা, আপনি কি মনে করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওরা অনেকটা এগিয়েছে?
আবার উদাসীনভাবে বোহর বললেন, আমার মনে করায় কী এসে যায়?
মোটকথা হতাশ হয়ে হেইসেনবের্গ ফিরে গেলেন। আসল কথা খুলে বলার মতো পরিবেশই খুঁজে পেলেন না তিনি। বস্তুত এই সাক্ষাৎকারে ভালোর চেয়ে মন্দই হল বেশি। নীলস্ বোহরের ধারণা হল নাৎসি বৈজ্ঞানিকরা অনতিবিলম্বে পরমাণু বোমা তৈরি করে ফেলবে। না হলে ওকথা বলল কেন হেইসেনবের্গ?
এই সাক্ষাৎকারের পরেই বোহর-এর এক বন্ধু গোপনে এসে খবর দিলেন তাকে গ্রেপ্তার করার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বোহর সুইডেনে পালিয়ে গেলেন। সেখান থেকে প্লেনে করে ইংল্যান্ডে। পরে আমেরিকায়। নীলস বোহর বহু সম্মান পেয়েছেন জীবনে–তার ভিতর একটি তার প্লেনে করে ইংল্যান্ডে আসার সময়। ব্রিটিশ এয়ারচিফ এই মূল্যবান কমডিটিটিকে নিরাপদে সুইডেন থেকে ইংল্যান্ডে আনবার ব্যবস্থায় এতই সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন যে, তাকে একটি বোমারু বিমানে করে নিয়ে আসা হয়। বৃদ্ধকে বসতে বলা হল প্যারাসুট এবং লাইফ-বেল্ট সেঁটে, বোমার গর্তটায়। বিস্মিত বোহর প্রশ্ন করলেন–এ কি! ওইখানে বসব কেন? গর্তের ভিতর?
পাইলট সবিনয়ে বললে, সেই রকমই নির্দেশ আছে স্যার! আমার প্লেন আক্রান্ত হলে আমি আপনাকে জীবন্ত বোমার মতো সমুদ্রে ফেলে দেব। আদেশ আছে, প্লেনটা ভেঙে গেলেও আপনাকে বাঁচাতে হবে। পিছন-পিছন আসছে একটা সি-প্লেন, সে আপনাকে উদ্ধার করবে!
ইংল্যান্ডে পৌঁছে জার্মান ইউরেনিয়াম-প্রোজেক্ট সম্বন্ধে প্রফেসর বোহর যা বললেন, তাতে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকা নূতন করে শুনল হুঙ্কার–কাগুজে বাঘ-এর!
৫. কী ১০-১৩
১০.
বারোই জুন 1943। লস অ্যালামস থেকে দুদিনের জন্য ছুটি নিয়ে ওপেনহাইমার এসেছে সানফ্রানসিস্কোয়। উঠেছে একটা হোটেলে। ওর স্ত্রী রয়েছে লস-অ্যালামস-এ। হঠাৎ কেন ওকে সানফ্রানসিস্কো আসতে হল? তা কেউ জানে না। এমনকি মিসেস ওপেনহাইমারও নয়। হোটেল থেকে রাত আটটা নাগাদ বের হল ওপেনহাইমার। একটা ট্যাক্সি নিল। ড্রাইভারকে বলল, চল-টেলিগ্রাফ হিল।
রবার্ট জে ওপেনহাইমার স্বপ্নেও ভাবেনি, ও ট্যাক্সি ডাকার সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠল রাস্তার ওপাশে একটা গাড়ির চালক। লোকটা তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করে চলেছে আজ চার মাস। লস অ্যালামস থেকে একই ট্রেনে সে এসেছে সানফ্রানসিস্কোয়। লোকটার নাম ডি-সি। একজন এফ. বি. আই. এজেন্ট। কর্নেল প্যাশ নিযুক্ত।
এফ. বি. আই.-য়ের সুপারিশ অগ্রাহ্য করে বিশেষ ক্ষমতাবলে জেনারেল গ্রোভসস্ ওপেনহাইমারকে চাকরি দিয়েছেন। এ কাজের অধিকার তার ছিল। কিন্তু তাই বলে এফ বি. আই.-চিফ, তার কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হননি। যাকে ক্লিয়ারেন্স দেওয়া যায়নি, জাতির স্বার্থে তার ওপর নজর রাখবার আদেশ দিয়েছেন কর্নেল প্যাশকে। ওপেনহাইমারের প্রতিটি পদক্ষেপের রেকর্ড তৈরি হয়ে যাচ্ছে তার অজান্তে।
ট্যাক্সিটা টেলিগ্রাফ হিল-এর একটা বাংলো বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। ভাড়া মিটিয়ে ওপেনহাইমার ঢুকে গেল ভেতরে। ডি-সি সে বাড়ি থেকে একশ মিটার দূরে তার গাড়িটা পার্ক করে চুপচাপ বসে রইল টেলিফটো ক্যামেরা হাতে। রাত বারোটা নাগাদ বাড়ির আলো নিবে গেল। সারা রাত কেউ বার হল না বাড়িটা থেকে। পরদিন ভোরবেলা দরজা খুলে বার হয়ে এল ওপনেহাইমার এবং একটি বছর-বত্রিশের মহিলা। মেয়েটি গ্যারেজ থেকে গাড়ি বার করল –ওপেনহাইমারকে নিয়ে চলে গেল এয়ারপোর্ট-এর দিকে। প্লেন ধরে ওপেনহাইমার চলে গেল পূর্বমুখে।
পরদিন বিস্তারিত রিপোর্ট পৌঁছে গেল কর্নেল প্যাশ-এর টেবিলে, খানপাঁচেক ফটো সমেত। মেয়েটিকে সহজেই শনাক্ত করা গেল। ডক্টর মিস্ জীন ট্যাটল। নামকরা কম্যুনিস্ট।
29 শে জুন জি-টু ডিভিসনের ডেপুটি চিফ অফ স্টাফ কর্নেল প্যাশ একটি বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠিয়ে দিলেন নিউ ইয়র্কে তার বড়কর্তা কর্নেল ল্যান্সডেলের কাছে।
***
ঠিক দু-মাস পরে একদিন রবার্ট ওপেনহাইমারকে দেখা গেল সানফ্রানসিস্কোতে জি-টু ডিভিশনাল হেডকোয়ার্টার্সে লায়াল জনসনের কামরায়। জনসন ডি- সিলভার ওপরওয়ালা এবং কর্নেল প্যাশ-এর অধীনে নিযুক্ত। বারোই জুন রাত্রের রিপোর্টখানা ডি-সি এর মাধ্যমে ওপরে পাঠিয়েছিলেন, ফলে মিস ট্যাটল-সংক্রান্ত সংবাদ জানতে বাকি ছিল না লায়াল জনসনের। আপ্যায়ন করে বসালো সে লস অ্যালামসের ডিরেক্টারকে।
শোনা গেল, ওপেনহাইমারের আগমনের হেতু হচ্ছে রোজি লোমানিটজ। ছোকরার পিছনে লেগেছে এফ.বি.আই.। লোমানিটজ ছিল বার্কলেতে ওপির ছাত্র, বর্তমানে লস অ্যালামসে। তাকে নাকি এফ. বি. আই. থেকে ধরে এনেছে জিজ্ঞাসাবাদ করতে। তাই প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টার স্বয়ং এসেছেন পুলিস হেডকোয়াটার্সে তত্ত্ব-তালাশ নিতে।
জনসন কম্যুনিস্ট-প্রভাবের কথা আলোচনা করল, বললে লোমানিজকে আপাতত নাকি ছাড়া যাচ্ছে না। আরও জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে তাকে। জনসনের ধারণা রীতিমত একটা গুপ্তচরবাহিনী ম্যানহাটান ডিস্ট্রিক্ট-এ গোপনে কাজ করে যাচ্ছে। তারা ডলারে মাইনে পায় না, পায়, রুবলস-এ।
ওপেনহাইমার গম্ভীর হয়ে বললে, আমি তোমার সঙ্গে একমত ক্যাপ্টেন। এমন ইঙ্গিত আমিও পেয়েছি।
–আপনি? কী ব্যাপার?
–জর্জ এলটেন্টনের নাম শুনেছ?
-বলেন কী! তার ফাইলটা আমি সপ্তাহে তিনবার ওল্টাই। নামকরা রাশান-এজেন্ট।
–সেই এলটেন্টন একজন দালালকে পাঠিয়েছিল লস অ্যালামসে। কার্যোদ্ধার হয়নি, কিন্তু সে তিন-তিনটে দরজায় ধাক্কা দিয়েছিল।
-বলেন কী! একটু বিস্তারিত করে বলবেন?
–বলতেই তো এসেছি–
আদ্যোপান্ত ঘটনাটা শুনে জনসন বললে, প্রফেসর এটা এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যে, আমার বস কর্নেল প্যাশ আপনার মুখ থেকে সরাসরি শুনতে চাইবেন।
–আমার আপত্তি নেই আবার বলতে। কর্নেল প্যাশ তার চেম্বার আছেন?
-না, ডক্টর। উনি একটা জরুরি কাজে বেরিয়েছেন। আপনি কাল সকালে একবার আসতে পারবেন?
–পারব। আটটার সময়। বিকালের প্লেনে আমি ফিরে যাব।
কর্নেল প্যাশ তার ঘরেই ছিলেন। কিন্তু ইচ্ছে করে কিছুটা সময় নিল তীক্ষ্ণধী জনসন। সে মনে মনে ছক কষে ফেলেছে। ওপেনহাইমার ফিরে যেতেই সে কর্নেল প্যাশ-এর ঘরে ঢুকল। বিস্তারিত বলল সব কথা খুলে। কর্নেল প্যাশ বললে, এখনই ওকে ডেকে নিয়ে এলে না কেন?
–কিছু ইলেকট্রিক্যাল গ্যাজেট লাগাতে হবে স্যার। ডক্টর ওপেনহাইমারের স্টেটমেন্টটা টেপ-রেকর্ড করে রাখতে চাই।
প্যাশ খুশি হল তার অধীনস্থ কর্মচারীর দূরদর্শিতায়।
পরদিন ওপেনহাইমার যখন কর্নেল প্যাশ-এর ঘরে ঢুকল তখন সে জানত না, রুদ্ধদ্বার কক্ষে সে যা বলছে তা গোপনে টেপ-রেকর্ড হয়ে রইল এফ. বি. আইয়ের দপ্তরে। কর্নেল প্যাশ আন্দাজ করেছিল, কোনো কাউন্টার-এসপায়োনেজের সূত্রে ওপেনহাইমার জানতে পেরেছিল, তাকে সন্দেহ করছে এফ. বি. আই.। তাই সে নিজে থেকেই ভালমানুষি দেখাতে এসেছিল জি-টু সদর দপ্তরে। আসলে লোমানিটজ-এর বিষয়ে তত্ত্বতালাস নিতে সে আদৌ আসেনি এবার সানফ্রানসিস্কোতে। এসেছিল পুলিসের সঙ্গে দহরম-মহরম করতে।
ওপেনহাইমারের গল্পটা ছিল এইরকম–এটেন্টনের দালাল লস অ্যালামসে। তিন-তিনজন বৈজ্ঞানিককে পর্যায়ক্রমে যাচাই করে। তিনজনই তাকে প্রত্যাখ্যান করেন। ঐ তিনজন বৈজ্ঞানিকের নাম, অন্তত দালালটির নাম, জানবার জন্য প্যাশ খুব পীড়াপীড়ি করে; কিন্তু কিছুতেই সেকথা বলতে রাজি হলেন না ওপেনহাইমার। তার যুক্তি-দালালটি আসলে নিতান্ত ভালামানুষ–ব্যাপারটার গুরুত্ব না বুঝেই সে এমন কাজ করেছে। তার কোনো অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না–আর বৈজ্ঞানিক তিনজন তো প্রত্যাখ্যানই করেছেন। ফলে তাঁদের আর মিছে কেন জড়ানো?
পরদিনই কথোকথনের টেপ-এর একটা কপি সমেত দীর্ঘ রিপোর্ট পাঠিয়ে দিল প্যাশ তার উপরওয়ালা কর্নেল ল্যান্সডেল-এর কাছে–নিউইয়র্কে। তার রিপোর্টের উপসংহারে প্যাশ লিখেছিল
“ This office is still of the opinion that Oppenheimer is not to be fully trusted and that his loyalty to the nation is divided. It is believed that the only undivided loyalty that he can give is to Sci ence and it is strongly felt that if in his position the Soviet Gov ernment could offer more for the advancement of his scientific cause, he would select that Government as the one to which he could express his loyalty.”
অর্থাৎ: ওপেনহাইমারকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না। জাতির প্রতি তার অকুণ্ঠ আনুগত্য নেই। তার একমাত্র লক্ষ্য : বিজ্ঞান। আজ যদি সোভিয়েট গভর্নমেন্ট তাকে বিজ্ঞানচর্চায় বেশি সুযোগ দেবার লোভ দেখায়, তবে সে অনায়াসে ও-পক্ষে যোগ দেবে!
অনতিবিলম্বে ল্যান্সডেল ডেকে পাঠালেন ওপেনহাইমারকে। পুনরায় জেরা। নানাভাবে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। ওপেনহাইমার দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করল, ঐ তিনজন বৈজ্ঞানিক অথবা ঐ দালালটির নাম প্রকাশ করে দিতে। বলল, আপনাদের সঙ্গে সব রকম সহযোগিতা করতে আমি প্রস্তুত–এজন্য স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এ কথা বলতে এসেছিঃ কিন্তু তাই বলে যাঁরা অপরাধী নন তাদের নাম আমি কিছুতেই বলব না।
ল্যান্সডেল বললেন, ঠিক আছে, ঠিক আছে। না বলতে চাইলে আর কী করব আমরা? এটা তো নাৎসি জার্মানি অথবা স্তালিনের রাশিয়া নয়। আপনাকে কোনোভাবেই বিব্রত করব না আমরা। খুশি হয়ে ওপেনহাইমার ফিরে গেল লস অ্যালামসে। মিস্ ট্যাটলকের প্রসঙ্গ আদৌ উঠল না।
***
ওখানেই কিন্তু মিটল না ব্যাপারটা। সমস্ত কাগজপত্র এফ. বি. আই. পাঠিয়ে দিল জেনারেল গ্রোভসকেটেপ রেকর্ড, মিস্ ট্যাটলকের ফটো সমেত। লিখল, আমাদের আপত্তি সত্ত্বেও আপনি ব্যক্তিগত দায়িত্বে ওপেনহাইমারকে নিযুক্ত করেছিলেন। আমরা আবার সুপারিশ করছি–তাকে অবিলম্বে বরখাস্ত করুন। এছাড়া আমাদের আরও তিনটি দাবি; প্রথমত-মিস্ ট্যাটলকের সঙ্গে কেন ওপনেহাইমার রাত কাটালেন? দ্বিতীয়ত-ঐ তিনজন বৈজ্ঞানিক কে? তৃতীয়ত–ঐ দালালটি কে? এ তিনটি প্রশ্নের জবাব আপনার অধীনস্থ কর্মচারীর কাছ থেকে জেনে আমাদের জানান। ব্যাপারটার গুরুত্ব যথেষ্ট। আপনার রিপোর্ট পেলে আমরা যুদ্ধসচিবের কাছে আমাদের রিপোর্ট পাঠাব।
জেনারেল গ্রোভসস-এর মানসিক অবস্থা সহজেই অনুমেয়। ম্যানহাটান ততদিন প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে। শিকাগোতে ফের্মি ‘চেন-রিয়্যাকশন’ সাফল্যমণ্ডিত করেছেন। ইউ-238 থেকে ইউ-235 পরমাণু পৃথকরণও করা গেছে। প্লুটোনিয়াম পরমাণু বিদীর্ণ করার ফর্মুলাও আবিষ্কৃত। এইসব তাত্ত্বিক সূত্রের সাহায্যে লস অ্যালামসে হাতে-কলমে বোমা প্রস্তুত হচ্ছে। সে কাজ যে তত্ত্বাবধান করছে, সে লোকটা রবার্ট জে. ওপেনহাইমার। ক্লাউস ফুকস্ ইতিমধ্যে হিসাব কষে বার করেছেন বোমার আকার, ওজন ও আকৃতি অর্থাৎ ‘ক্রিটিক্যাল সাইজ। ওপেনহাইমার বিভিন্ন বিভাগে তার অংশ তৈরি করেছেন। এ অবস্থায় ওপেনহাইমার সম্পূর্ণ অনিবার্য। অথচ
গ্রোভস্ ডেকে পাঠালেন ওপিকে। খোলাখুলি বললেন, তোমার বিরুদ্ধে অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ আছে। আমাকে সব কথা খুলে বলতেই হবে। বল, কে ঐ দালাল, কোন্ তিনজন বৈজ্ঞানিককে যাচাই করেছিল সে।
জবাবে ওপেনহাইমার যা বলেছিল, সেটাই তার জীবনে সবচেয়ে বড় মিথ্যাভাষণ।
তিনজন বৈজ্ঞানিকের মধ্যে দুজনের নাম সে বলেনি, বলেছিল মাত্র একজনের নাম। সে নামটা: রবার্ট জে, ওপেনহাইমার। দালালের নামটাও প্রকাশ করে দিয়েছিল সে এবার। তার নাম হাকন শেভেলিয়ার।
সজ্ঞান মিথ্যাভাষণ! বাস্তবে যা হয়েছিল তা এই : অন্য দুজন বৈজ্ঞানিক অলীক!
হাকন শেভেলিয়ার ওর দীর্ঘদিনের বন্ধু। ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের অধ্যাপনা করছেন 1938 থেকে। ওপনেহাইমারের ঝোঁক ছিল সাহিত্যের প্রতি। কাব্যপাঠে তার সখ ছিল। শুধু ইংরাজি নয়, ফ্রেঞ্চ ও জার্মান সাহিত্যও পড়তেন তিনি। এমন কি সংস্কৃতও। যত্ন নিয়ে সংস্কৃত শিখেছিলেন। সেই সূত্রেই এই দার্শনিক মনোভাবাপন্ন নির্বিরোধী সাহিত্যের অধ্যাপকটির সঙ্গে আলাপ। কৈশোরে এবং যৌবনে ওপেনহাইমার সাম্যবাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন একথা তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। সেই আমলেই এটেন্টনের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল শেভেলিয়ার এবং ওপির। কিছুদিন আগে লস অ্যালামস থেকে ওপেনহাইমার সস্ত্রীক ক্যালিফোর্নিয়াতে এসেছিলেন। পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন শেভেলিয়ার সস্ত্রীক। সন্ধ্যাবেলা। দুটি মহিলা বসে ড্রইংরুমে গল্প করছেন–ওপেনহাইমার উঠে গেলেন প্যানট্রিতে, ককটেইল বানিয়ে আনতে। গল্প করতে করতে শেভেলিয়ারও উঠে এলেন। ওপি ডিক্যানটারে ড্রাই মার্টিনী ঢালছেন, হঠাৎ শেভেলিয়ার বললেন, এলটেন্টনকে মনে আছে তোমার?
মুখ না ঘুরিয়েই ওপেনহাইমার বললেন, বিলক্ষণ। কেন?
কদিন আগে সে এসেছিল আমার কাছে। তোমার খোঁজ করছিল।
–কেন? কোনো প্রয়োজনে?
–না, ঠিক প্রয়োজনে নয়। বলছিল, রাশিয়া এবং আমেরিকা যদিও এ যুদ্ধে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে লড়াই করছে, তবু দু-দেশের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান হচ্ছে না।
অন্যমনস্কের মতো ওপেনহাইমার বলেন, তাই নাকি?
–নয়? তুমি কি মনে কর না–তোমরা যেসব আবিষ্কার করছ রাশিয়ান বৈজ্ঞানিকদের তা জানা উচিত এবং তারা যা বার করছে তা তোমাদের জানা উচিত?
এইবার ওপি তাকিয়ে দেখল বন্ধুর দিকে। হেসে বললে, তুমি কি চাও আমি পরমাণু বোমার ফর্মুলা ওদের দিয়ে দিই?
–আমি চাই, একথা বলছি না। তবে এলটেন্টন নিশ্চয় তাই চায়। রাশিয়াতে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি কতটা হয়েছে তাও সে জানাতে চায়।
এর জবাবে ওপেনহাইমার বাস্তবে কী বলেছিলেন তা নির্ধারিত হয়নি। শেভেলিয়ারের মতে–”আমার যতদূর মনে পড়ে, ওপি বলেছিল–ওভাবে খবর আদানপ্রদান করা ঠিক নয়।“ ওপেনহাইমারের মতে, আমি দৃঢ়স্বরে বলেছিলাম—“সেটা তো বিশ্বাসঘাতকতা!”
মোটকথা এখানেই কথোপকথনের সমাপ্তি। ওঁরা ড্রইংরুমে ফিরে আসেন এবং পরস্পরের স্বাস্থ্যপান করেন।
মজা হচ্ছে এই যে, ওপেনহাইমার সন্দেহাতীতরূপে জানতেন যে, দার্শনিক প্রকৃতির হাকন শেভেলিয়ার আদৌ গুপ্তচরের বৃত্তি নিয়ে ও প্রসঙ্গ তোলেননি’ নিছক কথার কথা হিসাবে ‘অ্যাকাডেমিক আলোচনা করেছিলেন বন্ধুর সঙ্গে। ওপেনহাইমার যদি উৎসাহিত হতেন তবে হয়তো তিনি বলতেন–তাহলে তোমরা পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ কর। রাশিয়ার তথ্য সংগ্রহ কর, তোমাদের তথ্য ওদের জানাও!
ওপেনহাইমারের এই স্বীকারোক্তির ফলাফল শেভেলিয়ারের জীবনে মারাত্মকভাবে প্রতিফলিত হয়। তৎক্ষণাৎ তাকে বরখাস্ত করা হল অজ্ঞাত কারণে–এবং প্রথম শ্রেণির ডিগ্রি থাকা সত্ত্বেও কোনো অজ্ঞাত কারণে তিনি কোথাও চাকরি জোগাড় করতে পারেননি বাকি জীবনে! প্রাইভেট টুইশানি করে জীবন কাটিয়েছেন। দীর্ঘ দশ বছর ধরে শেভেলিয়ার জানতে পারেননি তার কারণ। এ দশ বছরে বন্ধু ওপেনহাইমারের সঙ্গে দেখাও হয়েছে বেকার দুর্দশাগ্রস্ত শেভেলিয়ারের। ওপেনহাইমার শুধু মৌখিক সহানুভূতি জানিয়েছেন।
দীর্ঘ দশ বছর পরে আসল ব্যাপারটা জানতে পেরেছিলেন (ভেলিয়ার দম্পতি। যুদ্ধ শেষে যখন ওপেনহাইমারকে উঠে দাঁড়াতে হয়েছিল আসামির কাঠগড়ায়, রাষ্ট্রের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে ফ্রান্স বসে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় বেকার মানুষটা পড়েছিলেন আমেরিকায় ও গনহ, ইমারের বিচার কাহিনি। জবানবন্দিতে নিজ নামটা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। স্ত্রীকে কে বলে উঠেছিলেন, ওগো শুনছ! এই দেখ, কেন আমার করি। গিয়েছিল।
বন্ধুর সঙ্গে শেভেলিয়ারের আর কোনোদিন সাক্ষাৎ বা পত্রালাপ হয়নি।
জেনারেল গ্রোভসস্ মিস্ ট্যাটলকের প্রসঙ্গ আদৌ তোলেননি। কে ওপেনহাইমার ঐ মহিলাটির সঙ্গে রাত কাটিয়েছিলেন সৌজন্যবোধে তিনি তা জানতে চাননি। তবে দশ বছর পরে কর্নেল প্যাশ যখন বিচারকের সামনে তার যাবতীয় নথিপত্র দাখিল করেন তখন ওপেনহাইমারকে সব কথা স্বীকার করতে হয়।
.
১১.
বারোই এপ্রিল 1945। সকাল সাতটা বেজে নয় মিনিট।
ঘটনাটা বর্ণনা করবার আগে তার পটভূমিটা একবার ঐতিহাসিক মূল্যায়নে ঝালিয়ে নেওয়া ভাল। জার্মানির অবস্থা সঙ্গীন। বার্লিনের পতন হতে বাকি আছে মাত্র আঠারোটি দিন। ওদিক থেকে রাশিয়ান রেড আর্মি, আর এদিক থেকে জেনারেল প্যাটনের থার্ড আর্মি বার্লিনের টুটি টিপে ধরেছে। যে কোনোদিন যুদ্ধ শেষ হয়ে যেতে পারে-’ভি-ডে’ পালনের আদেশ এসে যেতে পারে। জাপানেরও নাভিশ্বাস উঠেছে পৃথিবীর অপর প্রান্তে। তিল তিল করে জাপানের মূল ভূখণ্ডের দিকে এগিয়ে চলেছে মার্কিন বাহিনী।
যে কথা বলছিলাম। ঠিক সাতটা বেজে নয় মিনিটে ডায়াসের উপর উঠে দাঁড়ালেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস-প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান। সেই ইতিহাসের ক্যাবিনেট রুম। উপরে ঝুলছে উড্রো উইলসনের তৈলচিত্র। ঘরে রুজভেল্ট-ক্যাবিনেটের সব কয়জন সভ্য। গত রাত্রে মারা গেছেন রুজভেল্ট। তার মরদেহ তখনও মাটির বুকে ফিরে যায়নি। চিফ জাস্টিস হারলান স্টোনের হাত থেকে বাইবেলটা নিয়ে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন ভাইস-প্রেসিডেন্ট–আই, হ্যারি এস. ট্রুম্যান, ডু সলেলি সোয়্যার…
সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান। দশ মিনিটের ভেতরেই শেষ। পূর্ববর্তী ক্যাবিনেটের সদস্যরা একে একে ঘর ছেড়ে বার হয়ে গেলেন। হারল্ড আইকস, হেনরি ওয়ালেস, হেনরি মর্থে্নথাও…ইত্যাদি ইত্যাদি।
ঘর ফাঁকা হয়ে গেলে ডায়াস থেকে নেমে এলেন সদ্যনিযুক্ত প্রেসিডেন্ট এবং তখনই তার নজরে পড়ল কোণায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন একজন। একমাথা সাদা ধপধপে চুল, বলিরেখাঙ্কিত বৃদ্ধ–হেনরি স্টিমসন, যুদ্ধসচিব।
–আপনি যাননি?
–যাবার উপায় নেই। অত্যন্ত জরুরি একটা কথা আপনাকে এখনই জানাতে
চাই।
-যুদ্ধের সব কথাই তো জরুরি।
-না, যুদ্ধক্ষেত্রের কথা নয়। এখানকার কথাই। আপনার মনে আছে প্রেসিডেন্ট-এনকোয়ারি কমিটির চেয়ারম্যান ক্যাবিনেট-সদস্য হ্যারি ট্রুম্যানের বাড়িতে গিয়ে তাকে আমি একটি ব্যক্তিগত অনুরোধ করেছিলাম।
–আছে মিস্টার সেক্রেটারি। ম্যানহাটান-প্রজেক্ট! যেখানে কোটি কোটি ডলার খরচ হয়েছে অথচ এক আউন্সও ফিনিশড প্রডাক্ট বার হয়নি।
-ইয়েস! ম্যানহাটান-প্রজেক্ট।
ঘড়ির দিকে এনজর দেখে নিয়ে ট্রুম্যান বললেন, দু-মিনিটের মধ্যে মূল তথ্যটা বলুন।
–ম্যানহাটান-প্রজেক্টে পরমাণু বোমা তৈরি হচ্ছে, সত্যিই কোটি কোটি ডলার ব্যয়ে। আমাদের আশা চারমাসের মধ্যে সেটা তৈরি হয়ে যাবে। একটি বোমায় হয়তো লক্ষ লোককে হত্যা করা যাবে। অসীম শক্তিশালী এই বোমা!
ম্লান হাসলেন হ্যারি ট্রুম্যান। বললেন, মিস্টার সেক্রেটারি। আমার অভিনন্দন! আশ্চর্য! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস-প্রেসিডেন্টকে পর্যন্ত এখবরটা জানাননি। কে কে জানেন?
তার চেয়ে শুনুন- কে কে জানেন না। ডগলাস ম্যাকআর্থার জানেন না, জেনারেল প্যাটন জানেন না, আইসেনহাওয়ার জানেন না,
-চার্চিল জানেন?
–জানেন।
–স্তালিন?
–না।
***
চিঠি লেখা হল। সেই চিঠিখানা নিউইয়র্কের হোয়াইট-হাউসে পৌঁছাল এপ্রিলের বারো তারিখ।
কর্মভার বুঝে নিতে দিন সাতেক সময় লাগল ট্রুম্যানের। যুদ্ধসচিব কিন্তু নাছোড়বান্দা। প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে এত বড় একটা ব্যাপার তিনি কিছুতেই আর গোপন রাখবেন না। অগত্যা সময় করে নিয়ে পঁচিশে এপ্রিল 1945 সকালে ট্রুম্যান বসলেন যুদ্ধসচিবের সঙ্গে ম্যানহাটান-প্রকল্পের কথা আলোচনা করতে। সে আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন আর একজন মাত্র তৃতীয় ব্যক্তি–জেনারেল গ্রোভস।
প্রেসিডেন্ট প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, এ প্রকল্পে হাত দেওয়া হল কার পরামর্শে?
গ্রোভস্ ফাইল থেকে একটি চিঠি মেলে ধরলেন। দীর্ঘ পত্র। লিখেছেন আলবার্ট আইনস্টাইন, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে। তারিখটা দোসরা অগাস্ট 1939। তার লাল পেন্সিলে দাগ দেওয়া কয়েকটা ছত্রের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলেন প্রেসিডেন্ট :
“…it has been made probable–through the work of Joliot in France as well as Fermi and Szilard in America… that it may be come possible to set up a nuclear chain reactions in a large mass of uranium… This new phenomenon would also lead to the con struction of bombs… extremely powerful bombs….” ‘জুলিও-ৎজিলাৰ্ড-ফের্মি সব অচেনা নাম, ‘চেন রিয়্যাকসান-অফ ইউরেনিয়াম’ ব্যাপারটা বোঝা গেল না–কিন্তু শেষ পংক্তিটা বুঝতে পারলেন ট্রুম্যান–অসীম শক্তিধর বোমার জন্ম হতে পারে।
–কিন্তু কী হবে এ বোমা দিয়ে? জার্মানির পতন হতে তো আর এক সপ্তাহ। প্যাসিফিক-ফ্রন্ট থেকেও যে খবর পাচ্ছি–
বাধা দিয়ে অভিজ্ঞ স্টিমসন বলেন, প্রেসিডেন্ট! এই পরমাণু বোমার ব্যবহার করবো কি করবো না, করলে কেমন করে, কোথায় করবো তা স্থির করতে পারে একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি। তাদের সুপারিশ আপনি মানতেও পারেন, নাও মানতে পারেন
–ঠিক কথা। এমন একটি কমিটি তৈরি করুন তাহলে।
–আপনার এইরকম অভিরুচি হতে পারে মনে করে আমি পূর্বেই একটি খসড়া তৈরি করে এনেছি। এতে পাঁচজন সদস্য আছেন।
প্রেসিডেন্ট কমিটি সভ্যদের নাম অনুমোদন করলেন। পাঁচজনই সমর-বিশারদ। বৈজ্ঞানিকদলের একজনও ছিলেন না কমিটিতে–অর্থাৎ যে বৈজ্ঞানিকদল প্রত্যক্ষভাবে পরমাণু-বোমা তৈরি করছিলেন।
ঐ পঁচিশে এপ্রিলই গঠিত হয়ে গেল ‘ইন্টেরিম কমিটি।
*
পঁচিশে এপ্রিল তারিখটা বুঝে নিতে আবার একবার পৃথিবীর উপর চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। ঐ দিন:
ইতালির গণ-অভ্যুথান হল। গুপ্তআবাস থেকে ফ্যাসিস্ট বেনিতো মুসোলিনি আর তার শয্যাসঙ্গিনী ক্লারাকে বের করে আনলো উন্মত্ত বিদ্রোহীরা। হত্যা করে ‘পাবলিক স্কোয়ার’-এ ঠ্যাঙ ধরে ঝুলিয়ে দিল, মাথা নিচের দিক করে।
জার্মানিতে ঐ একই দিনে রাশিয়ান লালফৌজ বার্লিন উপকণ্ঠে প্রথম প্রাচীর ভেঙে ভেতরে ঢুকল। ঈভা ব্রাউন এলেন বার্লিন-বাঙ্কারে হিটলারের পরিণাম ভাগ করে নিতে।
জাপানে ব্যাপক বোমাবর্ষণে ঐ দিন ধূলিসাৎ হয়ে গেল টোকিওর অনেকটা এলাকা।
মারিয়ানায়–অর্থাৎ হাওয়াই এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের মাঝামাঝি প্রশান্ত মহাসাগরের একটি নির্জন দ্বীপে–ঐ দিন 509 নং কম্পোসিট গ্রুপ পারমাণবিক বোমার সাময়িক পান্থশালাটি নির্মাণ শেষ করল।
যাই হোক, ইন্টেরিম কমিটির দ্বিতীয় মিটিং বসল পেন্টাগনে, ত্রিশে মে। কমিটির সদস্যেরা বললেন-বৈজ্ঞানিক দলের ভিতর থেকে কিছু বিশেষজ্ঞকে কমিটিতে কোঅপ্ট করা দরকার। না হলে এই বোমা নিয়ে কী করা উচিত তা ওঁরা নির্ধারণ করতে পারছেন না! তৎক্ষণাৎ সদস্য সংখ্যায় যুক্ত হল আরও চারটি নাম। কম্পটন, ফের্মি, লরেন্স এবং ওপেনহাইমার। শেষোক্ত ব্যক্তি বাদে তিনজনই বিজ্ঞানে নোবেল-লরিয়েট।
ওই চারজন ছাড়া বাদবাকি কেউই সেদিন জানতেন না অ্যাটম বোমা সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে কিনা। প্রস্তুত হওয়ার আগেই একটি কমিটি নির্ধারণ করতে বসেছেন–কোথায় ওটা ফেলা হবে। খবরটা ওঁরা পেতে শুরু করলেন ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে।
ওয়াইৎসেকার একজন অতি উচ্চপদস্থ মার্কিন সামরিক অফিসারকে এই সময় গাউডসমিটের রিপোর্টখানা দেখিয়ে বলেছিলেন, এতদিনে নিশ্চিত হওয়া গেল কী বলেন? জার্মান জুজুর আর ভয় নেই। আমাদেরও তাহলে এই নারকীয় কাণ্ডটা করতে হবে না।
অভিজ্ঞ সামরিক অফিসারটি জবাবে বলেছিলেন, তাই কি হয় স্যার? এত খরচ পড়ল যার পেছনে সেটা ব্যবহারই হবে না? দেখবেন, বোমা ঠিকই পড়বে।
অবাক হয়ে গিয়েছিলেন ওয়াইৎসেকার।
***
বস্তুতপক্ষে এই বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের পরিণাম সম্বন্ধে অনেক প্রথম শ্রেণির বৈজ্ঞানিকই ততদিনে ভাবতে শুরু করেছেন। বিশেষ করে গাউডসমিট-এর রিপোর্ট পাওয়ার পরে। এঁদের মধ্যে প্রফেসর নীলস বোহর, ৎজিলাৰ্ড, ফ্রাঙ্ক, রোবিনোভিচ ইত্যাদি মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাদের প্রচেষ্টার কথা একে একে বলি।
সর্বপ্রথম এ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছিলেন দার্শনিক প্রকৃতির প্রফেসর বোহর। পরমাণু-বোমা তৈরি হবার ঠিক এক বছর আগে তিনি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সঙ্গে দেখা করেন ছাব্বিশে অগাস্ট 1944-এ। একটি সুলিথিত স্মারকলিপি ধরিয়ে দেন প্রেসিডেন্টের হাতে। এই রিপোর্টে বোহর প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করেন অনাগত পরমাণু-বোমা প্রয়োগের বিষয়ে চিন্তা করতে। প্রফেসর বোহর রাজনীতিক ছিলেন না–কিন্তু এই রিপোর্টে তিনি অদ্ভুত দূরদর্শিতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন। একস্থানে তিনি বলেছেন, বিশ্বাস সৃষ্টিকারী আক্রমণকারীদের স্বপ্ন ইতিমধ্যে ভেঙে গেছে। তাদের পতন অনিবার্য এবং আসন্ন। কিন্তু আমার আশঙ্কা হয়, যে সব জাতি এ আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে আজ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করছে যুদ্ধান্তে তাদের মধ্যেও মতবিরোধ দেখা দেবে–কারণ। তাদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণার মধ্যে মৌল পার্থক্য আছে।
এজন্য বিশ্বশান্তির মুখ চেয়ে তিনি মিত্রপক্ষের তিন শীর্য-শক্তির ভিতর এই অসীম শক্তিধর অস্ত্রের বিষয়ে একটা সমঝোতায় আসতে প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দিয়েছিলেন।
প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এইভাবে গোপন সাক্ষাৎকারের কোনো রেকর্ড রেখে যাওয়া পছন্দ করতেন না। নীল বোহরের সঙ্গে আলোচনার সময় তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না কেউ। প্রেসিডেন্ট কাউকে বলে যাননি তাদের কী কথাবার্তা হয়েছিল। যুদ্ধান্তে প্রফেসর বোহর-কে এ বিষয় প্রশ্ন করা হলে নৈতিক কারণে তিনি কোনো জবাব দিতে অস্বীকার করেন। বলেন, প্রেসিডেন্ট যখন তা বলে যাননি–তখন আমার কিছু বলা শোভন হবে না।
মোটকথা, প্রেসিডেন্ট এ বিষয়ে অগ্রসর হয়ে কিছু করলেন না। নীলস বোহর অতঃপর চার্চিলের সঙ্গে দেখা করেন। সে সাক্ষাৎকারের সময় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা লর্ড চেরওয়েলও উপস্থিত ছিলেন। প্রফেসর বোহর পরমাণু-বোমার ফলশ্রুতি সম্বন্ধে দীর্ঘ আধঘন্টা ধরে বলেন। ধৈর্য ধরে এতক্ষণ শুনছিলেন চার্চিল। হঠাৎ তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। লর্ড চেরওয়েলকে বলেন : লোকটা কী বলতে চায়? রাজনীতি না পদার্থবিদ্যা?
What is he really talking about? Politics or Physics?
নীলস বোহর এ ব্যাপারে কী বলবেন ভেবে পাননি।
***
মর্মাহত হয়েছিলেন আলেকজান্ডার সাও। পারমাণবিক-বোমা প্রায় তৈরি হয়ে এল অথচ জার্মানি বা জাপান তা তৈরি করেনি জেনে ধনকুবের সাও রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়েন। তার মনে হয় বর্তমান যুদ্ধে এ অস্ত্র ব্যবহৃত হলে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যুর জন্য তিনিই পরোক্ষভাবে দায়ী হয়ে থাকবেন। তিনি প্রেসিডেন্টকে একটা খসরা দাখিল করেন 1944-এর ডিসেম্বরে।
তার প্রস্তাবটা ছিল–মিত্রশক্তি এবং নিরপেক্ষ দেশগুলির বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক, ধর্মজগতের প্রধান ও আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিদের সামনে এই অস্ত্রের কার্যকারিতা পরখ করে দেখানো হবে। এভাবে এ অস্ত্রের প্রয়োগক্ষমতা প্রমাণ করে জার্মানি ও জাপানকে চরমপত্র দেওয়া উচিত নির্দিষ্ট তারিখের ভেতর আত্মসমর্পণের নির্দেশ জানিয়ে।
এ পত্রটিও রুজভেল্ট বিবেচনার জন্য রেখেছিলেন তার দপ্তরে। যুদ্ধসচিবকে এর কথাও কিছু বলে যাননি।
পরমাণু-বোমার প্রয়োগের বিরুদ্ধে সবচেয়ে উদ্যোগী হন হাঙ্গেরিয়ান বৈজ্ঞানিক ৎজিলাৰ্ড। 1939 সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে তিনিই ছুটে গিয়েছিলেন আইনস্টাইন-এর কাছে। এবার 1945-এ তিনি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ চিত্র মানসচক্ষে দেখে শিউরে উঠলেন। তার মনে হল, এ বোমার জন্য তিনিই একান্তভাবে দায়ী। বোমা যাতে বর্ষিত না হয় সেজন্য প্রাণপাত করেছিলেন। ৎজিলাৰ্ড। ক্রমাগত চেষ্টা করেও হ্যাঁরী ট্রম্যানের সঙ্গে কোনো সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে পারলেন না তিনি। অতিব্যস্ত প্রেসিডেন্ট তার সাক্ষাৎপ্রার্থীকে পাঠিয়ে দিলেন জেমস বার্নের্স-এর কাছে। বার্নের্স একজন ক্ষমতাশালী ডেমোক্র্যাট সেনেটর। বস্তুত ওৎজিলার্ডের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের এক-সপ্তাহের ভিতরেই তিনি সেক্রেটারি অফ স্টেট পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।
ৎজিলাৰ্ড মানবিকতার দোহাই পেড়ে ধুরন্ধর বার্নের্সকে কাবু করতে পারলেন না। অবশেষে অন্য যুক্তির অবতারণা করলেন তিনি, আমার মনে হয় এখনই রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের চুক্তিবদ্ধ হওয়া উচিত। আমি স্যার, বর্তমান বিশ্বযুদ্ধের কথা ভাবছি না। ভাবছি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা।
বার্নের্স হেসে বলেছিলেন, তাহলে বলব, বড় তাড়াতাড়ি ভাবছেন আপনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধই এখনও শেষ হয়নি। আর ফর যোর ইনফরমেশন, প্রফেসর, রাশিয়ায় ইউরেনিয়াম আদৌ নেই।
হতাশ হয়ে ফিরে এলেন ৎজিলাৰ্ড লস অ্যালামসে। দেখলেন, সেখানে তাঁর সহকর্মী বৈজ্ঞানিকরা অনেকেই তার সঙ্গে একমত। তাঁরা বলছেন, জার্মানি যখন পরাজিত, জাপান নতজানু, তখন এ বোমা বর্ষণের কোনো অর্থই হয় না।
কে একজন (নামটা জানা যায়নি) বলেছিলেন, কর্তৃপক্ষ যদি আমাদের যুক্তি না শোনেন তবে আমরা এ কারখানায় ধর্মঘট করব। মার্কিন সরকার আমাদের সঙ্গে অলিখিত ভদ্রলোকের চুক্তি করেছিলেন যে, এ অস্ত্র শুধুমাত্র আত্মরক্ষার্থে ব্যবহৃত হবে- আগ্রাসী রণনীতির জন্য নয়। সরকার যদি চুক্তি না মানেন তবে সেটা হবে সরকারের চরম বিশ্বাসঘাতকতা!
ফুকস্ নাকি জবাবে বলেছিলেন, এখন এ প্রকল্প যে অবস্থায় আছে তাতে আন্ডার-গ্র্যাজুয়েটদের দিয়েই বাকি কাজটা সম্পন্ন করা সম্ভব। নাট-বোল্টুগুলো তো শুধু কষতে বাকি, বন্ধু!
লস অ্যালামসে সেদিন রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনেকক্ষণ এ নিয়ে আলোচনা হল। শিবিরে ইতিমধ্যে দুটি দল হয়ে গেছে। একদলের নেতা ওপেনহাইমার,–সে দলে আছেন ইন্টেরিম কমিটির বাকি তিনজন সদস্য–ফের্মি, কম্পটন আর লরেন্স। অপর দল বোমাবিরোধী। সে দলের দলপতি অভিজাত জার্মান বৈজ্ঞানিক নোবেল-লরিয়েট জেমস্ ফ্রাঙ্ক এবং তার সক্রিয় কর্তা ৎজিলাৰ্ড। ঐরাত্রেই সাতজন বৈজ্ঞানিক তৈরি করলেন একটি রিপোর্ট। তার নাম ফ্রাঙ্ক রিপোর্ট। তাতে সই দিলেন–ফ্রাঙ্ক, ৎজিলাৰ্ড, রোবিনোভিচ এবং আরও চারজন। রিপোর্টখানি নিয়ে ৎজিলাৰ্ড উপস্থিত হলেন ক্লাউস ফুকস-এর চেম্বারে। কিন্তু সই দিতে অস্বীকার করলেন ফুকস।
-কেন? আপনি তো বোমাবর্ষণের বিরুদ্ধে বলেই চিরকাল জানতাম আমি।
–আজ্ঞে না! ভুল জানতেন! এই বোমা তৈরি করতে দুই বিলিয়ন ডলার খরচ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। বুঝেছেন? দুই বিলিয়ন ডলার।
-তাহলে আপনি কি কিছুই করবেন না?
–কেন করব না? জাপান যখন জ্বলবে তখন বেহালা বাজাব। নীরোও তো তাই করেছিলেন। এই তো ইতিহাসের শিক্ষা।
ঝড়ের বেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন ৎজিলাৰ্ড। শেষদিকে ফের্মি মত বদলেছিলেন। তিনি এবং আই রাবি একটা যৌথ পত্র লিখেছিলেন প্রেসিডেন্টকে, “এই অস্ত্রের বিধ্বংসী ক্ষমতার কথা মনে করে আমরা পরামর্শ দিই নৈতিক কারণে এর প্রয়োগ আপনি বন্ধ করুন।”
নীলস বোহর-এর পত্র, ফ্রাঙ্ক রিপোর্ট, ফের্মির চিঠি–কিছুতেই কিছু হল না। আরও একটা চেষ্টা করেছিলেন ওৎজিলাৰ্ড। একক প্রচেষ্টা। গাড়ি নিয়ে একাই চলে গিয়েছিলেন লং-আইল্যান্ডের দক্ষিণতম প্রান্তে। এবার বাড়িটা চিনতে অসুবিধা হয়নি। বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক এবার সহজেই চিনতে পারলেন ৎজিলাৰ্ডকে। ছয় বছর আগে তাকে দেখেছিলেন, সে ওঁর ছাত্র। আদ্যোপান্ত সব কথা খুলে বললেন ৎজিলাৰ্ড। আইনস্টাইন তৎক্ষণাৎ রাজি হলেন পুনরায় রুজভেল্টকে একটি পত্র লিখতে।
25 মার্চ 1945 চিঠি লেখা হল। সেই চিঠিখানি নিউ ইয়র্কের হোয়াইট-হাউসে পৌঁছাল এপ্রিলের বারো তারিখ। কিন্তু প্রাপকের হাতে সেটা পৌঁছল না। পূর্বরাত্রে চিঠির প্রাপক ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট অন্তিম নিশ্বাস ফেলেছেন। চিঠিখানা রাখা ছিল, না-খোলা অবস্থায়, তার স্থলাভিষিক্ত হ্যারি ট্রুম্যানের টেবিলে। অপাত্রের হাতে। নিতান্তই নিয়তির পরিহাস!
.
১২.
পাঁচই জুলাই 1945। তিনখানি টেলিগ্রাম করলেন ওপেনহাইমার। একই বয়ান। প্রাপক তিনজন হচ্ছেন শিকাগোর আর্থার কম্পটন, বার্কলের আর্নেস্ট লরেন্স এবং নিউইয়র্কের লেসলি গ্রোভ। তিনজনেই আমেরিকান। টেলিগ্রামের বক্তব্য ‘পনের তারিখের পরে মাছ ধরতে যাব। বৃষ্টি না পড়লে পরদিনই মাছ ধরা যায়।
তিনজনেই প্রস্তুত ছিলেন। সাঙ্কেতিক ভাষার বক্তব্য বুঝলেন। রওনা হলেন দেখতে।
তিনটি বোমা তৈরি হয়েছে এতদিনে। দুটি প্লুটোনিয়াম পরমাণুর, একটি ইউরেনিয়ামের। সর্বমোট খরচ হয়েছে প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা। অঙ্কশাস্ত্রের হিসাবে তিনটিই ব্রহ্মাস্ত্র। তবে সব কিছু খাতায়-কলমে।
প্রশ্ন মাত্র একটাই : ফাটবে তো?
স্থির হল, একটিকে ফাটিয়ে পরখ করা হবে। লস অ্যালামস থেকে 339 কিমি দক্ষিণ-পশ্চিমে জনমানবহীন এক বিজন প্রান্তরে। জায়গাটার নাম অ্যালমগডো। মাস-ছয়েক আগেই স্থানটি নির্বাচিত হয়েছিল। ছয়মাস ধরে যাবতীয় ব্যবস্থা করা হচ্ছে ঐ মরুপ্রান্তরের গভীরে। সে ব্যবস্থার একটু পরিচয় দিই।
যেখানে বোমাটা ফাটবে তাকে বলা হল ‘গ্রাউন্ড জিরো’। প্রশ্ন হল : কতদূরে রাখা হবে যন্ত্রপাতি? মানুষের পক্ষেই বা নিরাপদ দূরত্ব কতটা? পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণের পূর্বঅভিজ্ঞতা তো কারও নেই! আন্দাজে ভুল হলে যে শেষ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরাই উড়ে যাবেন!! কী করা যায়? সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব ছিল ক্রিস্টিয়াকোস্কির নেতৃত্বে গঠিত একটি বিশেষ কমিটির উপর। কিস্টি ছিলেন বিস্ফোরক-বিশারদ। কিস্টি বললেন, প্রথমে একটি নমুনা বোমা ফাটাও। সাতই মে সেই বোমা ফাটানো হল–পরমাণু বোমা নয়, একশ-টন ওজনের ডিনামাইট স্তূপ। তার বিস্ফোরণের নিখুঁত হিসাব করা হল। এবার ‘স্কেল ফেলে’ কতদূরে কে থাকবেন স্থির করা হল। পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণ ক্ষমতা হিসাবমতো হবে 5,000 টন টি.এন.টি.র সমান। অর্থাৎ 50 গুণ সব কিছু বাড়ানো হল। নমুনা-বোমার যে যন্ত্রটা এক কিমি দূরত্বে নিরাপদ মনে হয়েছে তাকে পরমাণু বোমার ক্ষেত্রে 50 কিমি দূরে বসাতে হবে!
***
নির্ধারিত দিনে প্রায় আড়াই শতজন বৈজ্ঞানিক সমবেত হলেন ‘ট্রিনিটি-টেস্ট’ দেখতে। দুর্ভাগ্যক্রমে বৃষ্টি শুরু হল। আবহাওয়াবিদরা বললেন, রাত দুটোর পর আকাশ পরিষ্কার হয়ে যাবে। গ্রাউন্ড-জিরো থেকে দশহাজার গজ দূরে (প্রায় নয় কিলোমিটার) তিনটি অবজারবেশন পোস্ট তৈরি হয়েছে। বিশেষভাবে নির্মিত ভূগর্ভস্থ গুহায়। এখানে কয়েকটি যন্ত্রের মাধ্যমে রেকর্ড করা হবে বিস্ফোরণের ফলাফল। বেস-ক্যাম্পের দূরত্ব ষোলো কিলোমিটার। সেখানে ফাঁকায় দাঁড়ানো-না দাঁড়ানো নয়, শোওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ঐ দশ হাজার গজ দূরে থেকে বোতাম টিপে রেডিও-র মাধ্যমে বোমাটাকে ফাটানো হবে। তাই বলে অত দামি জিনিসটাকে তো বিনা রক্ষকে ফেলে রাখা যায় না। তাই স্থির হয়েছে। দু-জন মেশিনগানধারীসহ দুঃসাহসী ক্রিস্টিয়াকৌস্কি ঐ বোমার কাছে পাহারা দেবেন পাঁচটা পর্যন্ত। এঞ্জিন-চালু অবস্থায় একটা জিপ খাড়া থাকবে। ঠিক পাঁচটায় ওঁরা রুদ্ধশ্বাসে জিপে করে পালাবেন। কিস্টি পাকা ড্রাইভার। আধঘন্টায় অনায়াসেই পৌঁছে যাবেন ষোলো কিলোমিটার দূরের নিরাপদ বেস ক্যাম্পে।
কে যেন বলল, কিন্তু ধরুন জিপটা যদি যান্ত্রিক গণ্ডগোলে অচল হয়ে পড়ে?
গ্রোভস্ বলেন, সে কথাও ভেবেছি আমি। তাই তো কিস্টিকে পছন্দ করলাম। ও ভাল দৌড়ায়। কলেজ স্পোর্টস-এ প্রাইজ পেয়েছে। এবার প্রাইজটা তো বড় সামান্য নয়–ওর প্রাণ-কিস্টি আধঘন্টায় নিরাপদ দূরত্বে যাবেই।
ওপেহাইমারকে দশ হাজার গজ দূরত্বে ভূগর্ভস্থ কক্ষে রেখে গ্রোভূস্ চলে গেলেন বেস ক্যাম্পে। অনেকেই আছেন সেখানে। প্রত্যেককে নির্দেশ দেওয়া। হয়েছিল–গণনা শুরু হতেই মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে হবে। ঠ্যাঙ বোমার দিকে, মাথা উল্টোদিকে। কানে তুলো। চোখ বন্ধ। তার উপর হাত চাপা দিতে হবে। আলোর ঝলকানি চুকে যাওয়ার পর ওদিকে তাকাতে পার–তবে খালি চোখে নয়, বিশেষ পদ্ধতিতে বানানো গগলস পরে। প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছে। সেই চশমা।
ঘোষক গুনতি শুরু করল 5-10 মিনিট থেকে। প্রথমে পাঁচ মিনিটের তফাতে, পরে প্রতি মিনিটে। পাঁচটা উনত্রিশে মিনিটের প্রতি সেকেন্ডে।
পাঁচটা উনত্রিশেও কিন্তু জিপটা এসে পৌঁছাল না। উত্তেজনায় ছটফট করছে সবাই। স্যাশ অ্যালিসন নির্বিকারভাবে সেকেন্ড ঘোষণা করে চলছে: উনষাট… আটান্ন…সাতান্ন….
মাত্র ত্রিশ সেকেন্ড বাকি থাকতে জিপটা এসে থামল। পড়ি-তো-মরি করে তিনজনে ঢুকে পড়লেন ভূগর্ভস্থ নিরাপদ কক্ষে।
নয়… আট….সাত….
সবাই উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন চোখ-কান বন্ধ করে।
একটিমাত্র ব্যতিক্রম। একজন এ আদেশ মানেননি। সজ্ঞানে। সাত সেকেন্ড বাকি থাকতে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠেন তিনি। বলে ওঠেন : দুত্তোর! দশ মাইল দূরত্বে এখানে ঘোড়ার ডিম হবে।
নোবেল লরিয়েট লরেন্স শুয়ে ঠিক পাশেই। কানে তুলো গোঁজা, তবু শুনতে পেলেন তিনি কথাটা। কে এমনভাবে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল বুঝতে পারলেন না। মুখ তুলতেও সাহস হল না-: চার ….তিন….দুই….
চীৎকার করে ওঠেন আর্নেস্ট লরেন্স, শুয়ে পড়ো! মরবে তুমি!
লোকটাও চীৎকার করে ওঠে: কী বকছেন স্যার পাগলের মত।
তৎক্ষণাৎ চিনতে পারেন লরেন্স। কিন্তু জবাব দেবার সময় ছিল না। ঘোষক বললে, নাউ।
***
ট্রিনিটি-টেস্ট-এ যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা পরে সাংবাদিকদের জানিয়েছিলেন। বৈজ্ঞানিক ছাড়া একজন মাত্র সাংবাদিককে এ পরীক্ষায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তিনি নিউ ইয়র্ক টাইমস্-এর উইলিয়াম লরেন্স। সকল বর্ণনাই এক সুরে বাঁধা। সুপারলেটিভের ছড়াছড়ি। সেটাই স্বাভাবিক। অভিধান হাতড়ে কেউ উপযুক্ত বিশেষণ খুঁজে পাননি।
ফাইনম্যানের কথা বলি। একমাত্র তিনিই সোজা দাঁড়িয়ে ওদিকে চোখ বুজে তাকিয়েছিলেন। অভিজ্ঞতাটা উনি এমনভাবে বর্ণনা করেছেন: মুহূর্তে সব সাদা হয়ে গেল। যেন অজস্র সূর্য একসঙ্গে আকাশে উঠেছে! চোখ ঝলসে গেল। চোখে ও মাথায় যন্ত্রণা বোধ হল। আমার চোখ বন্ধ ছিল, গগলস-এর নিচে। তাতেই ঐ অনুভূতি হল আমার। পরমুহূর্তেই যন্ত্রণা সত্ত্বেও আমি চোখ খুললাম। সাদা আলোটা ততক্ষণে হলুদ হয়ে গেছে। প্রকাণ্ড একটা ধোঁওয়ার বলয় পাক খেতে খেতে ওপরে উঠে যাচ্ছে। ধোঁয়ার ঐ কুণ্ডলিগুলি ওপরে কমলা রঙের আর একটা আগুনের বলয়–তার কিনারগুলো সিঁদুরে লাল। ওপরে ওপরে আরো ওপরে উঠে গেল। অনাবিষ্কৃত একটা নগ্ন সত্য প্রকাশিত হল যেন–পারমাণবিক বন্ধনমুক্ত মহামৃত্যু। অপূর্ব দৃশ্য! তারপর অস্বাভাবিক একটা নিস্তব্ধতা। আমাদের বেস ক্যাম্পের কেউ কোনো কথা বলেনি। পুরো দেড় মিনিট। তারপর এল বিস্ফোরণের শব্দটা!
দেড় মিনিট পরে। লরেন্স এতটা আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন যে, হঠাৎ বলে ওঠেন, ওটা কিসের শব্দ?
যেন এত বড় একটা বিস্ফোরণের পরে কোনো শব্দই হবে না!
ওপেনহাইমার দশ হাজার গজ দূরের ‘এম’-পয়েন্টে। মন্ত্রমুগ্ধের মত তিনি নাকি বলে ওঠেন :
“নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্টা হি ত্বাং প্ৰব্যথিতান্তরাত্মা ধৃতিং ন বিন্দামি শমং চ বিষ্ণো।”
–ইস দ্যাট গ্রিক প্রফেসর?– প্রশ্ন করেন জেমস ফ্রাঙ্ক।
–নো স্যার। ইটস স্যানস্কৃট! জবাব দিলেন ওপেনহাইমার!
–কী অর্থ কবিতাটার?
–হে পরমপিতা! আপনার আকাশস্পর্শী তেজোময় নানাবর্ণযুক্ত ঐ বিস্ফারিত মুখমণ্ডল এবং উজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে আমার হৃদয় আজ ব্যথিত। আমি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছি, আমি ‘শম’ অর্থাৎ শান্তি হারিয়ে ফেলেছি।
অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, আশ্চর্য কবিতা। ঐ কথাটাই ঠিক মনে হচ্ছিল আমার। জার্মান ভাষায় অবশ্য। এ বিস্ফোরণে একটা জিনিস হারিয়ে গেল শুধু–সেটা শান্তি! আমার হৃদয়ও আজ ব্যথিত।
গ্রোভস অনতিবিলম্বে একটি টেলিগ্রাফ করেন পটসড্যামে, যুদ্ধসচিব স্টিমসনকে–
“সন্তান নির্বিঘ্নে জন্মলাভ করেছে। স্বাস্থ্যবান শিশু। সে হাইহোল্ডে* [*হাইহোল্ড স্টিমসনের বাড়ি। গ্রোভসের অফিস থেকে তার দূরত্ব কত তা টেলিগ্রাফক্লার্ক না বুঝলেও স্টিমসন বুঝবেন।] থাকলেও এখানে বসে তাকে দেখতে পেতাম। তার চিল্লানি এখান থেকে আমার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছাবে।”
টেলিগ্রাফটা পাঠানো হল পটসড্যামে। জার্মানিতে। যুদ্ধসচিব তখন সেখানে। শুধু তিনি একা নন। হ্যারি ট্রুম্যানও। ঐ পটসড্যামে।
পটসড্যাম।
সাধারণজ্ঞানের প্রশ্নপত্রে প্রশ্নটা করে দেখবেন : পটসড্যাম কোথায়? কীজন্য বিখ্যাত?
শতকরা নিরানব্বই জন ছাত্র লিখবে নির্ভুল উত্তর-’বার্লিন শহরের দক্ষিণপশ্চিম শহরতলি। বার্লিনের পতনের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে এখানে বিজয়ী মিত্রপক্ষের শীর্ষ সম্মেলন হয়েছিল। এখান থেকেই জাপানকে নতজানু হবার আদেশ প্রচারিত হয়।
শতকরা একজন হয়তো ভুল উত্তর লিখে বসবে। খোঁজ নিয়ে দেখবেন, বেচারি ফিজিক্স কিংবা ম্যাথুসের। ভুল উত্তর লেখায় নিশ্চয় তাকে আপনি নম্বর দেবেন না। বোকাটা লিখেছে: পটসডামে আলবার্ট আইনস্টাইনের বাড়ি। বিতাড়িত হবার পূর্ব জীবনের কুড়িটি বছর তিনি ওখানে কাটিয়েছেন।
স্থান-কাল-পাত্র। একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। স্থানটাকে আপাতত ধ্রুবক বলে ধরে নিন–দেখবেন, পাত্র কাল এর সঙ্গে তাল রেখে চলছে। ধরুন কালটা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় দশক। দেখবেন, পটসড্যামের রাস্তায় সারি সারি পপলার গাছের তলা দিয়ে প্রত্যষে প্রাতভ্রমণে বার হয়েছেন একজন প্রোঢ়। সারা শহরতলি তখন ঘুমোচ্ছে, কুয়াশার ঘোর ভেদ করে পুবআকাশ থেকে সোনালি হাতছানি এসে পড়েছে ভ্রমণরত প্রৌঢ় মানুষটির কালো ওভারকোটে। ওঁর এক হাতে ছড়ি, অপরহাতে ধরা আছে কুকুরের চেন। মুখে মোটা চুরুট। সারা শহরতলি ঘুমোচ্ছে, শুধু কৌতূহলী একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছুটছে তাঁর পিছন পিছন–ওঁরই চুরুটের ধোঁয়া। অনুগামী ধূমকুণ্ডলী আর অগ্রগামী কুকুর, মাঝখান চলছেন আইনস্টাইন। শুধু ঐ কুকুরটাই নয়, প্রৌঢ় বৈজ্ঞানিককে পিছনে ফেলে আগে আগে ছুটছে আরও একটা জিনিস। সেটা ঐ বৈজ্ঞানিকের চিন্তাধারা। শুধু বৈজ্ঞানিককেই নয়, বিশ্বকেই যেন কয়েক দশক পিছনে ফেলে যেতে চায় সেটা।
বদলে দিন ‘কাল’টাকে। এগিয়ে আসুন দশক দুয়েক। আমাদের এ কাহিনির বর্তমান পটভূমিতে। 1945 সালের ষোলোই জুলাই। ট্রিনিটি টেস্টের ঐ চিহ্নিত দিনে। দেখবেন পাত্রও বদলে গেছে। পরিবেশটাও। সেই নীলআকাশ-সন্ধানী পপলারগুলি উলীত। শহরতলি ঘুমোচ্ছে না–সেটা শ্মশান। পথের ধারে ধারে আর কারনেশান-ডায়ান্থাস্- হলিহক নেই, আছে কংক্রিটের চাংক–ইটের স্তূপ আর মিলিটারি ডিসপোসালের শূন্যগর্ভ ক্যান। এবার পাত্রত্রয় হচ্ছেন বিজয়দপী তিন যুদ্ধবাজ–চার্চিল, ট্রুম্যান আর স্তালিন।
যুদ্ধের সময় তিন প্রধান একাধিকবার মিলিত হয়েছিলেন। কুইবেক-এ, তেহেরান-এ এবং ইয়ালটায়। ট্রুম্যান অবশ্য এই প্রথম যোগ দিচ্ছেন শীর্য সম্মেলনে; ইতিপূর্বে এসেছিলেন রুজভেল্ট। শেষ শীর্ষ সম্মেলনের জন্য চিহ্নিত হয়েছিল পরাজিত বার্লিন শহর। দুর্ভাগ্যবশত বার্লিনে এমন একখানা বড় বাড়ি নজর পড়ল না, যেখানে এত বড় সম্মেলন হতে পারে। সমস্ত শহর তখন ধ্বংসস্তূপ। তাই শহরপ্রান্তে ক্রাউন-প্রিন্স উইলহেলম-এর আবাসে আহত হল এই মহাসম্মেলন। ষোলোহ জুলাই প্রথম অধিবেশন বসার কথা, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, স্তালিন সময়মতো এসে পৌঁছাতে পারলেন না। কী করা যায়? সময় কাটাতে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান গেলেন বার্লিন শহর দেখতে। অর্থাৎ বার্লিনের ধ্বংসস্তূপ দেখতে। সঙ্গে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ। যুদ্ধসচিব স্টিমসন, সেক্রেটারি অফ স্টেট, নৌবিভাগের অ্যাডমিরাল লেহি প্রভৃতি। এ কাহিনির পক্ষে আপাতদৃষ্টিতে সেই ধ্বংসস্তূপ পরিদর্শনের বর্ণনা বাহুল্য মনে হতে পারে, কিন্তু বোধকরি এরও প্রয়োজন আছে। পরমাণু-বোমা ফেলবার চূড়ান্ত আদেশ যিনি দিয়েছিলেন, সেই মানুষটিকে ঠিকমত চিনে নিতে হলে এটাও উপেক্ষার নয়।
প্রেসিডেন্ট তার স্মৃতিচারণে বলেছেন, “একটা বাড়িও নজর পড়ল না যেটা অনাহত। সবকটিই ক্ষতিগ্রস্ত। হয় ধ্বংসস্তূপ, না হলে হাড়-পাঁজরা বার করে দাঁড়িয়ে আছে প্রেতের মতো। আমাদের গাড়ির ক্যারাভ্যান গিয়ে থামল রাইষ চ্যান্সলারির সামনে। সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। সেই ঝোলা বারান্দাটার চিহ্নমাত্র নেই–যেটির ওপর দাঁড়িয়ে হিটলার তার অনুগামী নাৎসি যুদ্ধবাজদের সামনে বক্তৃতা দিত।”
ট্রুম্যান তো আর সেই ফিজিক্স অথবা ম্যাথসের ছাত্রটি নন–তাহ খোঁজ করে দেখতে চাননি–আইনস্টাইনের বাড়িটা মুখ থুবড়ে পড়েছে অথবা ‘হাড়-পাঁজরা বার করে দাঁড়িয়ে আছে।
ভ্রমণকাহিনীর উপসংহারে ট্রুম্যান লিখেছেন
“It is a demonstration of what can happen when a man over reaches himself…. I never saw such destruction. I don’t know whether they learned anything from it or not.”
অর্থাৎ মানুষ তার ক্ষমতার বাইরে হাত বাড়ালে কী পায় তারই প্রদর্শনী যেন!… আমি এমন ধ্বংসস্তূপ কখনো দেখিনি। জানি না, ওরা এ থেকে আদৌ কোনো শিক্ষা পেল কিনা।
ইতিহাস এর জবাব দিয়েছে। ওরা কোনো শিক্ষা পাক আর না পাক, প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান যে কোনো শিক্ষাই পাননি তার প্রমাণ হিরোশিমা এবং নাগাসাকি!
When a man over-reaches himself….
পরদিন সতেরোই জুলাই সকালে মার্কিন যুদ্ধসচিব এসে দেখা করলেন প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের সঙ্গে। বাড়িয়ে দিলেন একটি টেলিগ্রাফ। তাতে লেখা–সন্তান নির্বিঘ্নে জন্মলাভ করেছে।
চার্চিল আনন্দে আত্মহারা। তখনই দেখা করলেন ট্রম্যানের সঙ্গে। পরামর্শ দিলেন–এ কথা স্তালিনকে ঘুণাক্ষরেও জানাবার প্রয়োজন নেই। তুরুপের টেক্কা লুকিয়ে রাখাটাই বুদ্ধিমানের কাজ। শুধু দেখতে হবে, রাশিয়া যেন এই শেষ মওকায় জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করে বসে। তাহলেই তাকে লুটের ভাগ দিতে হবে। জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার বর্তমানে আনাক্রমণাত্মক চুক্তি বজায় আছে। তাই থাক। স্তালিন যেন অ্যাটম বোমার কথা জানতে না পারে। ট্রম্যানের এটা ঠিক পছন্দ হল না। চার্চিল তাঁর সঙ্গে একমত হলেন না। ঐদিনই পটসড্যামে এসে উপস্থিত হলেন ইউরোপ-খণ্ডে মিলিত মিত্র বাহিনীর সেনাপতি জেনারেল আইসেনহাওয়ার। অ্যাটম-বোমার বিষয়ে বিন্দুবিসর্গও তিনি জানতেন না। সব কথা শুনে তিনি নাকি বলেছিলেন আশা করি এমন অস্ত্র আমাদের ব্যবহার করতে হবে না।
অথচ ঐদিনই ট্রুম্যান তাঁর দিনপঞ্জিকায় লেখেন—
“I then agreed to the use of the A-bomb if Japan did not yield.’
–অর্থাৎ সেই দিনই ঠিক করলাম জাপান আত্মসমর্পণ না করলে আমি। পরমাণু-বোমা ব্যবহার করব।
অবশেষে স্তালিন এসে পৌঁছালেন পটসড্যাম-এ। শুরু হল ঐতিহাসিক অধিবেশন। তিন রাষ্ট্রের প্রধান, তাঁদের ধুরন্ধর রাজনৈতিক সহকর্মী আর দোভাষীদের দল। যুবরাজ উইলহেমের ঐতিহাসিক প্রাসাদ গমগম করছে। যুদ্ধকালে এটা হাসপাতালরূপে ব্যবহৃত হয়েছিল। যুদ্ধান্তে হাসপাতাল সাফা করে এই সম্মলনের ব্যবস্থা হয়েছে। হাসপাতাল ছিল নাৎসি জার্মানির। জার্মানরা রাজপ্রাসাদের ভিতর একটি ফুলের বাগান বানিয়েছিল। এত বোমা-বর্ষণেও ফুলগাছগুলি নিঃশেষিত হয়নি। হল এই অনুষ্ঠানে। ফুলগুলো তুলে এনে ওরা বিজয়-উৎসবের তোড়া বাঁধল। হল-এর কেন্দ্রস্থলে রাখা ছিল এক হাজার জেরেনিয়াম ফুলের প্রকাণ্ড একটা ‘রেড স্টার’–স্তালিনকে সম্বর্ধনা জানাতে।
এক সপ্তাহে ধরে চলল অধিবেশন। পৃথিবীর ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হল। ফিলিপাইন, ভারতবর্ষ, পোল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, জার্মানির ভবিষ্যৎ লিপিবদ্ধ হল। স্তালিন বললেন, ইতিপূর্বে তিনি বলেছেন–জার্মানির পতনের তিন মাসের মধ্যেই তিনি জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। তিনমাস প্রায় পূর্ণ হয়ে এসেছে। এখন সময় হয়েছে নিকট, অনুমতি পেলেই তিনি জাপানের সঙ্গে বাঁধন ছিঁড়তে প্রস্তুত। চার্চিল ভাব দেখাচ্ছেন, তুমি আর কেন মিছে কষ্ট করবে ভাই? আমরা দুজনেই ব্যাপারটা ম্যানেজ করে নেব।
সম্মেলন শেষ হয়ে এল প্রায়। ট্রুম্যান প্রতিদিনই স্তালিনকে মারাত্মক সংবাদটি জানাবেন মনে করেন, অথচ হয়ে ওঠে না। চার্চিল এর ঘোরতর বিরোধী। হয়তো তাই ইতস্তত করছিলেন।
উনিশে জুলাই প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান সকলকে নৈশভোজে আপ্যায়ন করলেন। বিরাট আয়োজন। খানা আর পিনার অঢেল ব্যবস্থা। ডিনারের সময় পিয়ানো বাজাল মার্কিন বাহিনীর সার্জেন্ট ইউজিন লিস্ট। ভাল পিয়ানোর হাত ছিল ছোকরার। বাজালো ‘এ মাইনর’, ওপাস 42-এ শর্পা-র একখানা বিখ্যাত ওয়ালটজ। চমৎকার বাজালো। সঙ্গীত শেষ হতেই মহান নেতা স্তালিন প্রস্তাব করলেন, সঙ্গীতজ্ঞের সম্মানে ওঁরা তিন নেতা একটি ‘টোস্ট’ দেবেন। তৎক্ষণাৎ তিন নেতা মদের পাত্র হাতে এগিয়ে এলেন মার্চ করে। সার্জেন্ট লিস্ট-এর নাকের ডগায় এসে পানপাত্র তুলে ধরে তার স্বাস্থ্য পান করলেন। অ্যাডমিরাল লেহি তার স্মৃতিচারণে লিখেছেন–উৎসব শেষে সার্জেন্ট লিস্ট ওঁকে বলে, স্যার যুদ্ধের সময় অনেকবার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি, কিন্তু এমন আতঙ্কগ্রস্ত আমি জীবনে হইনি। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি স্তালিন, চার্চিল আর আমাদের প্রেসিডেন্ট মার্চ করে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন।
তার দুদিন পরে একুশে জুলাই ডিনার ‘থ্রো করলেন কমরেড স্তালিন। ট্রুম্যান সাহেবের ওপর টেক্কা ঝাড়লেন তিনি। আগেকার ভোজের থেকে পাঁচ কোর্স বেশি খাবার এল। শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যে তাঁর নির্দেশে একটি জঙ্গী বিমানে মস্কো থেকে এসে উপস্থিত হল শ্রেষ্ঠ পিয়ানোবাদকের দল। আগের দিন খানাপিনা মিটেছিল রাত একটায়–এবার রাত দেড়টা পর্যন্ত চলল সঙ্গীতের আসর। আধ ঘন্টা বেশি। চার্চিল মশাই নাকি গান ভালবাসেন নানা শেক্সপীয়র পড়ে কোনো অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে এটা আমি অনুমান করছি না। তিনি নিজেই তা লিখেছেন:
I was bored to tears. I don’t like music. I wanted to go home.
চার্চিল-সাহেব নাকি গানের মাঝপথেই উঠে চলে যেতে চেয়েছিলেন। ট্রুম্যান তাকে আটকে রাখেন, বলেন এটা খারাপ দেখাবে।
তার দুদিন পরে চরম প্রতিশোধ নিলেন সিংহশিশু চার্চিল। এবার তিনি হলেন নিমন্ত্রণকর্তা। লন্ডন থেকে এল রয়্যাল এয়ারফোর্সের পিয়ানো-বাদকের দল। অ্যাডমিরাল লেহি লিখেছেন, ‘গান যেমনই হক, চার্চিল সাহেবের কড়া হুকুম ছিল; রাত দুটোর আগে যেন গান-বাজনার আসর না ভাঙা হয়। সিগারেটসেবী ট্রুম্যান-সাহেবের উপর পাইপমুখো স্তালিন মেরেছিলেন টেক্কা। কিন্তু পিঠ তুলতে পারলেন না তিনি–চুরুটমুখো চার্চিল এবার ঝাড়লেন ছোট্ট একখানি দুরি। তুরুপের।
এদিকে ট্রুম্যানের অবস্থা সেই ‘ভবম-হাজামের মত। পেট ফুলছে ক্রমাগত। ফুলবেই। চার্চিলকে বলেছেন, চার্চিল বারণ করেছেন স্তালিনকে জানাতে–কিন্তু সামরিক শক্তি হিসাবে ব্রিটেনের চেয়ে রাশিয়ার স্থান অনেক উঁচুতে। তাই এতবড় খবরটা স্তালিনকে না বলা পর্যন্ত ঘুম হচ্ছিল না ট্রুম্যানের। তাতে চার্চিল চটে যায় তো যাক। কে জানে–এই নিয়ে যদি যুদ্ধোত্তর-দুনিয়ায় স্তালিনের সঙ্গে তার মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয়ে যায়? তখন তো চার্চিল পাঁচিলের ওপর বসে মিটিমিটি হাসবে।–এতবড় দায়িত্ব নিতে সাহস হল না ট্রুম্যানের। স্থির করলেন, খবরটা জানাবেন–তবে কায়দা করে। অর্থাৎ সময়, পরিবেশ আর ভাষার ভেতর থাকবে ওস্তাদি প্যাঁচ।’ধরি মাছ না ছুঁই পানি’ ভঙ্গিতে!
পরদিন চব্বিশে জুলাই–অর্থাৎ হিরোশিমায় বোমাবর্ষণের মাত্র তেরোদিন আগে–সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষিত হবার পর সবাই যখন একে একে চলে যাচ্ছেন তখন ট্রুম্যান গুটিগুটি এগিয়ে এলেন স্তালিনের কাছে। যেন মামুলি খোশ-খবর বলছেন, এমন ভঙ্গিতে বললেন, ‘ভাল কথা মনে পড়ল… ইয়ে হয়েছে….শুনেছি আমার বিজ্ঞানীরা নাকি একটা মারণাস্ত্র বার করেছেন যার অস্বাভাবিক বিস্ফোরণ শক্তি।
একনিশ্বাসে কথাটা বলে ট্রুম্যান হাসিহাসি মুখ করলেন। চার্চিল দাঁড়িয়ে ছিলেন পাশেই। ঊর্ধ্বমুখে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়ছিলেন নির্বিকারভাবে। যেন খবরটা নেহাৎই মামুলি। স্তালিন বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্য দেখালেন না। বললেন তাই নাকি? খুব আনন্দের কথা। ওটা ঐ বাঁটকুল জাপানিদের মাথার ঝাড়ুন তাহলে।
ভাষাটা আমি বানিয়েছি। হয়তো ঠিক এ ভাষায় কথোপকথা হয়নি। এই ঐতিহাসিক আলাপচারিতার কোনো ‘ডাইরেক্ট স্পীচ অফ ন্যারেশান’ অনেক খুঁজেও পাইনি। যা পেয়েছি তা এই:
ট্রুম্যান তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন
“On July 24 I casually mentioned to Stalin that we had a new weapon of unusual destructive force. The Russian Premier showed no special interest. All he said was that, he was glad 16 hear it and hoped we make good use of it against the Japanese,”
স্তালিন গাড়িতে উঠে রওনা দেওয়া মাত্র চার্চিল বললেন, মহান নেতা-সাহেব কী বললেন?
–কিছুই তো বললেন না। জানতেও চাইলেন না কী জাতের বিস্ফোরক!
চার্চিল তাঁর স্মৃতিচারণ গ্রন্থে বিস্ময় প্রকাশ করে লিখেছেন :
“Nothing would have been easier than for him to say : Thank you so much for telling me about your new bomb. I, of course, have no technical knowledge. May I send my experts in these nu clear sciences to see your experts tomorrow morning?”
“স্তালিন সহজেই বলতে পারতেন, ঐ বোমার কথা জানানোর জন্য ধন্যবাদ। আমি অবশ্য বিজ্ঞানের ব্যাপার ভাল বুঝি না। কাল বরং আমার পরমাণু-বিশারদ পদার্থ বিজ্ঞানীদের আপনার বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠিয়ে দিই, কী বলেন?”
চার্চিল তিনটি ভুল করেছেন। প্রথমত ট্রুম্যান ‘বোমা’ শব্দটা আদৌ ব্যবহার করেননি, বলেছিলেন ‘মারণাস্ত্র। দ্বিতীয়ত, পারমাণবিক’ শব্দটাও উচ্চারণ করেননি ট্রুম্যান-ফলে নিউক্লিয়ার পদার্থ বিজ্ঞানীদের’ প্রসঙ্গই ওঠে না। তৃতীয়ত, চার্চিল জানতেন না স্তালিনের এ ঔদাসিন্যের মূল কারণ কী! স্তালিন ন্যাকা সেজেছিলেন মাত্র। তিনি জানতেন সবই, এবং এও জানতেন যে, ঐ পারমাণবিক অস্ত্রের যাবতীয় সংবাদ তার গুপ্তচরবাহিনী সংগ্রহ করে যাচ্ছে। যথাসময়ে তার সবকটি খুঁটিনাটি জানতে পারবেন উনি।
সেয়ান সেয়ানে কোলাকুলির সময় এমনই হয়ে থাকে। কোন্ সেয়ান কোন্ সেয়ানকে লেঙ্গি মারছে কোনো সেয়ানই তা বুঝতে পারে না। সবাই ভাবে আমি বুঝি জিতলাম। লেঙ্গি যে আসলে মারছেন মহানেতা স্তালিন তা ট্রুম্যান টের পেলেন বেশ কিছুদিন পরে-ম্যাকেঞ্জি কিং-এর পত্র পেয়ে।
***
ওইদিনই ট্রুম্যান এবং স্টিমসনের কাছে এসে উপস্থিত হলেন মার্কিন স্থলবাহিনীর প্রধান জেনারেল মার্শাল এবং বিমানবাহিনীর চিফ জেনারেল আর্নল্ড। তারা জানতে চাইলেন–পারমাণবিক বোমা আদৌ ফেলা হবে কি না, হলে কবে হবে এবং কোথায় ফেলা হবে।
প্রথম দুটি প্রশ্নের জবাব পেলেন সহজেই : বোমা ফেলা হবে এবং যতশ্রীঘ্র সম্ভব। তৃতীয় প্রশ্নটির বিষয়েই বিস্তারিত আলোচনা হল। প্রথমে স্থির হয়েছিল এই পাঁচটি শহরের মধ্যে যে কোনো একটিতে ফেলা হবে সেই বিধ্বংসী বোমা-হিরোসিমা, ককুরা, নীগাতা, নাগাসাকি অথবা কিয়াতো। স্টিমসনের অনুরোধে শেষ নামটা বাতিল করা হল। ওখানে নাকি আছে প্রাচীনতম বৌদ্ধমন্দির–বহু শতাব্দীর স্মৃতিবিজড়িত স্বর্ণমন্দির।
একটিমাত্র পারমাণবিক বোমায় কতটা ক্ষতি হতে পারে সেটা নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে অনেক আগে থেকেই নির্দেশ জারি করা হয়েছিল–ঐ পাঁচটি শহরে আদৌ কোনো সাধারণ বোমা বর্ষণ করা হবে না। ঐ পাঁচটি শহরবাসী তাদের দুর্লভ সৌভাগ্যে এতদিন উৎফুল্ল ছিল। তাদের ধারণা–এটা নিতান্তই কাকতালীয় ঘটনা। তারা জানত না যে, তারা একদল সাইকোপ্যাথের জিয়ানো কই মাছ।
.
১৩.
ছাব্বিশে জুলাই পটন্ড্যাম থেকে ঘোষিত হল তিন বিশ্ববিজয়ীর শেষ চরমপত্র : অবিলম্বে জাপান যদি আত্মসমর্পণ না করে তবে চরম সর্বনাশ অনিবার্য।
তারপর যা ঘটেছে তা সর্বজনবিদিত ইতিহাস। বাস্তবপক্ষে স্তালিন জার্মানিতে এসে পট্ল্ড্যামে মিলিত হবার আগেই জাপান রাশিয়ার কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছিল–সে নাকি আত্মসমর্পণ করতে চায়। রাশিয়া যেন মধ্যস্থতা করে। স্তালিন জাপানকে সে সুযোগ দেননি। সে ইতিহাস আমি বিস্তারিত বলেছি আমার ‘জাপান থেকে ফেরা’ গ্রন্থে। পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মোটকথা জাপানের জবাব কী হবে তা ধরে নিয়েই যাবতীয় ব্যবস্থা ঘড়ির কাঁটা ধরে করা হচ্ছিল। গ্রোভস-এর। ভাষায়, ‘কোটি কোটি ডলার খরচ করে আমরা কী বানালাম তা পাঁচজনকে না দেখালে কৈফিয়ৎ দেব কী?’ অন্যত্র–
‘No need to get so excited! It’s better for a few thousand Japs to perish than a single of our boys.’
: ‘অতটা উত্তেজিত হবার কী আছে? আমাদের একটা ছোকরার প্রাণ রক্ষা করতে কয়েক হাজার জাপানিকে প্রয়োজন হলে প্রাণ দিতে হবে বৈকি।
এসব যুক্তি আপনারা শুনেছেন। খবরের কাগজে পড়েছেন। বোধকরি শোনেননি তার জবাবটা। খ্রিস্টান পাদরি শীল ওর প্রত্যুত্তরে যে কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন–
‘ঠিক ঐ যুক্তিই একদিন দেখিয়েছিলেন হিটলার-হল্যান্ডে বোমাবর্ষণের আগে, অথবা ইহুদি নিধনযজ্ঞকালে!
সে যাই হোক, ঘড়ির কাঁটা টিকটিক করে এগিয়ে চলেছে। জাপান জানে না, পৃথিবী জানে না সে কথা। প্রশান্ত মহাসাগরের এক অখ্যাত দ্বীপে একটি ব্রহ্মাস্ত্র। প্রহর গুনে চলছে। টাইম-বম্ব! কোনো দুর্ঘটনা না হলে সে বোমা ফাটবেই!
দুর্ঘটনা ঘটেছিল। একটা নয়–দু-দুটো। তবু হিরোশিমা মুক্তি পেল না।
প্রথম দুর্ঘটনা–’ইন্ডিয়ানাপোলিস্’ যুদ্ধ জাহাজ জাপানি সাবমেরিনে সলিলসমাধি লাভ করল। ঐ জাহাজেই পাঠানো হয়েছিল পরমাণু বোমাটিকে, আমেরিকার কোনো বন্দর থেকে প্রশান্ত মহাসাগরের নির্দিষ্ট দ্বীপপুঞ্জে। জাহাজের ক্যাপ্টেনও জানতো না, কি মহামূল্য সম্পদ সে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নৌবাহিনীর চিরাচরিত রীতি লঙ্ঘন করে তাকে যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তাতে সে স্তম্ভিত হয়ে গেছে! ডেক-এর উপর ঐ যে বিচিত্র বস্তুটি রাখা আছে ঐটাকে বাঁচাতে হবে–প্রয়োজনবোধে আকাপ্টেন জাহাজের সমুদয় নাবিকের জীবনের বিনিময়েও। জাহাজ ডুবে গেলেও ওটা সমুদ্রে ভাসবে এমন বন্দোবস্ত করা আছে। ইন্ডিয়ানাপোলিস এই অভিযান থেকে ফিরে আসেনি নিরাপদ বন্দরে–জাপানি সাবমেরিনে সেটা ডুবে যায়–কিন্তু নিরাপদে ওই অজানা বস্তুটি প্রশান্ত মহাসাগরের নির্দিষ্ট বন্দরে নামিয়ে ফিরে আসার পথে।
দ্বিতীয় দুর্ঘটনাটা রাজনৈতিক। চৌঠা জুলাই গ্রেট ব্রিটেনে গণভোট হয়। পটসড্যামে যখন মহাসম্মেলন চলছে তখন ব্রিটেনে ভোটের গুনতি হচ্ছে। চার্চিল নিশ্চিন্ত ছিলেন সাফল্যের বিষয়ে–এত বড় বিশ্বযুদ্ধে তিনি বিজয়ী। তবু ফলাফল ঘোষিত হবার পূর্বমুহূর্তে তিনি ফিরে এলেন স্বদেশে। ছাব্বিশে জুলাই মধ্যরাত্রে ঘোষিত হল পল্ড্যামের শেষ হুঙ্কার আর ঐ দিনই শেষ রাত্রে হল নির্বাচনের ফলাফল। চার্চিল হেরে গেছেন! বিকাল চারটার সময় চার্চিল এলেন বাকিংহাম প্যালেসে। পদত্যাগপত্র দাখিল করতে। এতবড় আঘাত আর অপমান তিনি কল্পনাই করেননি। বেরিয়ে যাওয়ার মুখে সাংবাদিকদের শুধু বলেছিলেন–”আমি দুঃখিত, যুদ্ধটা চূড়ান্তভাবে শেষ করার সুযোগ আমাকে দেশবাসী দিল না। তবে জাপানের পতন আসন্ন। আজ্ঞে হ্যাঁ আপনারা যত তাড়াতাড়ি ভাবছেন, তার আগেই। তার ব্যবস্থাও আমি করে এসেছি।
ছয়ই অগাস্ট, রাত্রি দুটো পঁয়তাল্লিশ মিনিট। তিনটি বিমান রওনা হল জাপানের দিকে। একটি বোমারু বিমান-নাম ‘এনোলা গে’। তার গর্ভে একটি মাত্র বোমা। প্রকাণ্ড বোমা, অথচ তার নাম লিটল বয়’!! তার পাইলট কর্নেল টিবেট এবং বোমারু ক্যাপ্টেন পার্সন জানে কী বস্তুটি। আর কেউ তা জানে না। সকাল আটটা পনেরো মিনিটে রেডিওতে নির্দেশ এল-নির্বাচিত তিনটি শহরের সবগুলিতেই যদি আবহাওয়া খারাপ থাকে তবে বোমাবর্ষণ না করেই ফিরে এস।
পরপর তিনটি শহরের নাম মনে আছে পাইলটের: হিরোসিমা, ককুরা আর নীগাতা।
নটা বেজে পনেরো। বিমান তখন 9,632 মিটার উঁচুতে, গতিবেগ ঘন্টায় 525 কিমি। পিছনে পিছনে আসছে দুটি ফাইটার প্লেন।
দূরে দেখা গেল হিরোশিমা। ইতিপূর্বে বোমাবর্ষণ হয়নি সেখানে। শহরবাসী নিশ্চিন্ত।
পার্সন বোতামটা টিপল। বোমাটা বেরিয়ে যেতেই খানিকটা লাফিয়ে উঠল প্লেনটা। পরক্ষণেই প্লেনের মুখটা ঘুরিয়ে দিল টিবেট। ফুলস্পীড! পালাও পালাও।
হঠাৎ আলোয় আলো হয়ে উঠল সমস্ত জগৎ। পরমুহূর্তেই একটা ধাক্কা খেল প্লেনটা। কয়েক সেকেন্ড পরে আবার একটা ধাক্কা। প্রথমটা প্রাথমিক বিস্ফোরণের। বিস্ফোরণ হয়েছে মাটি থেকে দু-হাজার ফুট (600 মিটার) ওপরে। দ্বিতীয়টা সেই বিস্ফোরণের প্রতিঘাত। পৃথিবীর বুকে আঘাত খেয়ে শব্দতরঙ্গের প্রতিধ্বনি। প্লেনটা তখন পনের মাইল (24 কিমি) দূরে।
পৃথিবীর বুক থেকে মুছে গেছে একটা জনপদ। তার নাম হচ্ছে, হচ্ছে নয়, ছিল–হিরোশিমা!
***
পরদিন সাতই অগাস্ট সকাল নয়টার সময় টোকিও শহরপ্রান্তে একটি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল একটি মিলিটারি জিপ। একজন মিলিটারি অফিসার এসে কড়া নাড়লেন দরজায়। কিমোবনা-পরা এক বৃদ্ধ বার হয়ে এলেন : কী চাই?
প্রফেসর নিশিনা, এখনই আমার সঙ্গে আসতে হবে। গতকাল থেকে আমরা হিরোশিমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করতে পারছি না। না টেলিফোনে, না রেডিওতে। এইমাত্র খবর পেলাম সেখানে নাকি একটা-আজ্ঞে হ্যাঁ, একটা মাত্ৰ-বোমা পড়েছে। তাতে শহরটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আপনি এসে দেখুন।
প্রফেসর য়োমিও নিশিনা হচ্ছেন জাপানের সবচেয়ে বড় নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট। নীলস বোহর-এর সঙ্গে কাজ করতেন। অটো হানের বন্ধু!
মুহূর্তমধ্যে তৈরি হয়ে নিলেন নিশিনা।
জিপে উঠতে যাবেন এক সাংবাদিক দৌড়ে এল। বললে, প্রফেসর, ওরা বলছে এটা পরমাণু বোমা। এইমাত্র মার্কিন ব্রডকাস্ট শুনে এলাম। নির্জলা মিথ্যা প্রচার। কী বলেন?
-আমি তো এখনও কিছুই দেখিনি। যা শুনছি তাতে মনে হয়…মিথ্যা নয়।
যা দেখলেন তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন প্রফেসর নিশিনা। তবু মনোবল হারাননি। সমস্ত দিন অম্লত অভুক্ত বৃদ্ধ প্রফেসর ধ্বংসস্তু’ পরিদর্শন করলেন, মাপ-জোখ নিলেন–যেস্থানের ওপর বোমাটা ফেটে পড়েছিল সেখানে মাটি খুঁড়ে রেডিও-অ্যাকটিভিটির পরিমাণ নিরূপণ করলেন নিজের বিপদ তুচ্ছ করে (চার মাস পরে তাঁর দেহে রেডিও-অ্যাকটিভিটির লক্ষণ দেখা যায় এবং দীর্ঘদিন তিনি নার্সিংহোমে চিকিৎসাধীন ছিলেন)। দুদিন পরে (9 অগাস্ট) ক্লান্তদেহে ফিরে এলেন যখন টোকিওতে, তখন উনি জানেন… তাপমাত্রা কতটা উঠেছিল, কত উঁচুতে বোমাটা ফেটেছিল, বায়ুর গতি কতটা হয়েছে, কতটা টি.এন.টি. বোমার বিস্ফোরণের সমতুল্য এই দুর্ভাগ্য। পরে হিসাব কষে দেখা গেছে প্রফেসর নিশিনার এই প্রাথমিক হিসাব নিখুঁত হিসাবের 97 শতাংশ নির্ভুল।
টোকিওতে ফিরে এসেও রেহাই নেই। মিলিটারির লোকেরা বাড়ি যেতে দিল না ওঁকে। সোজা নিয়ে গেল সমরদপ্তর।
একজন সামরিক বড়কর্তা বললেন, প্রফেসর। কতদিন লাগবে অমন বোমা তৈরি করতে? মাসছয়েক পর্যন্ত আমরা ওদের ঠেকিয়ে রাখতে পারি।
প্রফেসর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, বর্তমান পরিস্থিততে ছয় মাস কেন, ছয় বছর লাগা উচিত। আর আপনারা একটা কথা খেয়াল করছেন না–জাপানে। ইউরেনিয়াম ধাতু আদৌ নেই।
প্রফেসর। এই নতুন বিপদ থেকে উদ্ধারের কোনো পথই কি আপনি দেখাতে পারেন না? ক্লান্ত প্রফেসর বললেন, পারি। জাপান ভূখণ্ডের ওপর কোনো মার্কিন বিমান এসে পৌঁছাবার আগেই তাকে গুলি করে নামাতে হবে। সমুদ্রে।
এতক্ষণে নিশিনা ছুটি পেলেন। প্রায় মাতালের মতো টলতে টলতে ফিরে এলেন সমরদপ্তর থেকে নিজ আবাসে। বাড়িতে ঢুকেই দেখেন সেখানে অপেক্ষা করছেন দুজন সামরিক অফিসার। ওঁকে দেখেই একজন লাফিয়ে ওঠেন: প্রফেসর। এখনি আমার সঙ্গে একবার আসতে হবে। নাগাসাকির সঙ্গে আমাদের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ওরা কোনো সাড়া দিচ্ছে না। না টেলিফোন, না রেডিওতে! কী হতে পারে বলুন তো?
***
পরমাণু-বোমার সাফল্যে ম্যানহাটান-প্রজেক্টে যে অবিমিশ্র আনন্দের হিল্লোল বয়ে গিয়েছিল এমন কথা বলতে পারি না। ৎজিলাৰ্ড বলেছিলেন, ছয়ই অগাস্ট তারিখটা আমার জীবনে একটা কালো দিন। আইনস্টাইন, ফ্রাঙ্ক, রোবিনোভিচ প্রভৃতি মর্মাহত হয়েছিলেন এ সংবাদে। উইনি হিগিবথাম নামে একজন বৈজ্ঞানিক রেডিওতে খবর শুনে মাকে চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘যে কাজ এতদিন ধরে করলাম তার জন্য বিন্দুমাত্র গর্ববোধ করছি না। I am afraid that Gandhi is the only real disciple of Christ at present!’
আর একজন বাস্তুচ্যুত জার্মান কবি হেরম্যান হেজভর্ন লিখলেন একটা এপিক কবিতা
The Bomb that Fell on America
তার একস্থানের অনুবাদ :
“বোমাটি পড়ল মার্কিন মুলুকে–মাটিতে নয়, মাথায়।
কই? মানুষগুলো ছাই হয়ে গেল না তো?
যেমন গেছিল হিরোশিমায়?
না! মানুষের দেহ রইল অবিকৃত।
বিকৃত শুধু মন!
গলে পচে খসে পড়ছে মানুষের অন্তঃকরণ!
সর্বজনশ্রদ্ধেয় আর নরাধম এক সারিতে এসে দাঁড়াল।
হারিয়ে গেল একটা সেতু….অতীতের সঙ্গে বর্তমানের।
এতদিনের শক্ত পৃথিবীটা প্রকাণ্ড জেলির মত থকথকে।
ক্লেদাক্ত পূতিগন্ধময় কৃমিকুণ্ড একটা।
না! পৃথিবীটা নেই। হারিয়ে গেছে!
এ আমরা কী করলাম!
হে আমার স্বদেশবাসী। এ তোমরা কী করলে!”
এজাতীয় চিন্তা করার মানুষ কিন্তু মুষ্টিমেয়। লস অ্যালামসে অধিকাংশই সেদিন আনন্দে আত্মহারা। জ্বলন্ত মশাল হাতে শোভাযাত্রায় পথে নেমেছে সবাই। নাচে গানে হৈ-হল্লায় ফেটে পরছে। সবাই সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছে।
ক্লাউস ফুকস্ বললে, আজ উৎসব হবে। সারারাত সবাই নাচব। ভোজের আয়োজন কর। খানা, পিনা ঔর নাচনা! দাঁড়াও গাড়িটা বার করি। মদের বন্যা বইয়ে দেব।
ফুকস্ বেরিয়ে গেল তার গাড়িটা নিয়ে সান্তা-ফের দিকে। সান্তা-ফে লস অ্যালামস থেকে মাইল চব্বিশ ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই প্রচুর মদ কিনে ফিরে এল আবার। মধ্যরাত পর্যন্ত চলল মদ্যপানের আসর। একমাত্র প্রফেসর ফ্রাঙ্ক সস্ত্রীক উঠে চলে গিয়েছিলেন। এক লক্ষ জাপানির মৃত্যুকে মদ্যপানের মাধ্যমে অভিনন্দিত করতে তিনি গররাজি। ফুকস্ মদ নিয়ে ফিরে আসার পর উঠে গেলেন ৎজিলাৰ্ড আর ফাইনম্যান। তাঁরাও উৎসবে যোগদান করতে অস্বীকার করলেন। ফুকস্ বলে, প্রফেসর ৎজিলাৰ্ড!
ৎজিলাৰ্ড জবাব দিলেন না। নীরবে বেরিয়ে এলেন ব্যাঙ্কোয়েট হল ছেড়ে। উৎসব গৃহের বাইরে এসে দেখেন ফাইনম্যান অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনিও এ উৎসবে যোগদান করতে অস্বীকার করেছেন।
ৎজিলাৰ্ড ফাইনম্যানকে বললেন, আশ্চর্য। আমি ভাবতেই পারিনি ফুকস্ লোকটা এমন। লক্ষাধিক জাপানির মৃত্যুতে নোকটা পৈশাচিক উল্লাসে একেবারে নাচছে!
ফাইনম্যান বলেন, কেন প্রফেসর? আমি তো সেদিনই বলেছিলাম–
Fuchs/Looks/An ascetic/Theoretic!
***
পৃথিবীর অপর প্রান্তে ঐ ছয়ই অগস্টের রেডিও নিউজের প্রতিক্রিয়ার কথা বলি এবার :
ইংল্যান্ডে ‘ফার্ম হল’ কারাগারে সন্ধ্যা ছয়টার নিউজ বুলেটিন শুনে লাফিয়ে ওঠে কারারক্ষক মেজর রিটনার। রেডিও নিউজে বলছে, লর্ডস মাঠে অস্ট্রেলিয়া পাঁচ উইকেটে 265 করেছে। তার সঙ্গে একটা অদ্ভুত সংবাদ। আজ সকালে একটি মার্কিন বি-29 বিমান হিরোশিমায় একটা পারমাণবিক বোমা ফেলেছে। মুহূর্তমধ্যে এক লক্ষ জাপানি হতাহত। বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতা নাকি বিশ হাজার টি.এন.টি. বোমার সমতুল। জাপানে হিরোশিমা নামে কোনো শহর আজ আর নেই।
মেজর রিটনার লোভ সামলাতে পারে না। তার বন্দিশালায় তখন আটক আছেন পরাজিত জার্মানির সর্বশ্রেষ্ঠ নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্টবৃন্দ। যাঁদের তৈরি অ্যাটম বোমার ভয়েই এতদিন কাটা হয়ে ছিল মিত্রপক্ষ। মেজর রিটনার তৎক্ষণাৎ তলব করে বন্দিদলের বয়োজ্যেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকটিকে।
অনতিবিলম্বে লাঠি ঠুকঠুক করতে করতে এসে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ বৈজ্ঞানিক অটো হান। ইউরেনিয়াম-পরমাণুর হৃদয় যিনি সর্বপ্রথম সজ্ঞানে বিদীর্ণ করেছিলেন, সেই বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিক। রিটনার তাঁকে সমাদর করে বসালেন। খবরটা রসিয়ে রসিয়ে শোনালেন তাকে। শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন বৃদ্ধ অধ্যাপক। চুপ করে বসে রইলেন কয়েকটা মুহূর্ত–যেন মৌনতা অবলম্বন করছেন কোনো শোকের বার্তা শুনে। তারপর মুখ তুলে হঠাৎ বলেন, নিউজ-এ কি বলেছে, এটা পারমাণবিক বিস্ফোরণ?
-ইয়েস প্রফেসর।
বৃদ্ধ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন আবার। তারপর হঠাৎ কী যেন মনে পড়ে যায়। চমকে উঠে আবার বলেন, এক্সকিউজ মি! কী বললেন তখন? হান্ড্রেড থাউজেন্ড জাপানি মারা গেছে একটি বিস্ফোরণে?
-ইয়েস প্রফেসর। তাই তো বলল রেডিওতে।
হানড্রেড থাউজেন্ড! একলক্ষ!-বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াতে গেলেন। পারলেন না। টলে পড়লেন সোফায়। মেজর রিটনার ছুটে আসে। ওঁর নাড়ির গতি পরীক্ষা করে তৎক্ষণাৎ কিছুটা ব্রান্ডি খাইয়ে দেয়। বলে, আপনি এখানেই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করুন বরং…..
“থ্যাঙ্কু মেজর। হ্যাঁ তাই করতে হবে। আমি….ঠিক…মানে দাঁড়াতে পারছি না।
সন্ধ্যা সাতটায় বন্দিদের নৈশ আহার পরিবেশন করা হল। বন্দি-বিজ্ঞানীরা। যে-যার চিহ্নিত চেয়ারে গিয়ে বসলেন। ফন লে, ওয়াইৎসেকার, গেলার্চ, উইটজ, হেইসেনবের্গ প্রভৃতি। দলে ওঁরা দশজন। হঠাৎ সকলের নজর পড়ল টেবিলের মাঝখানের সিটটা খালি। প্রফেসর অটো হান আসেননি। তিনিই বয়োজ্যেষ্ঠ, সর্বজনশ্রদ্ধেয়। মাঝখানের চেয়ারখানা তাঁর।
ডক্টর কার্ল উইটজ বললেন, প্রফেসর হানকে মেজর রিটনার ডেকে পাঠিয়েছিল ঘন্টাখানেক আগে। এখনও ফিরলেন না কেন তিনি? তোমরা অপেক্ষা। কর, আমি ওকে নিয়ে আসি।
মিনিট-দশেক পবে ডক্টর উইটজ-এর কাঁধে ভর দিয়ে বৃদ্ধ অধ্যাপক এলেন।
–কী হয়েছে স্যার? আপনি কি অসুস্থ?
-না না, আমার কিছু হয়নি। একটা খবর আছে। এইমাত্র বি. বি. সি. রেডিও ব্রডকাস্ট করেছে….
খবরটা বিস্ফোরকের মতোই ফাটল-কিন্তু কেউ কোনো শব্দ করল না। পুরো দেড় মিনিট।
স্তব্ধতা ভেঙে প্রফেসর হানই প্রথম কথা বললেন। ইতিমধ্যে তিনি সামলেছেন অনেকটা। হেসে বললেন, হেইসেনবের্গ, মাই বয়। তুমি হেরে গেছ। আমেরিকান বৈজ্ঞানিকদের কাছে। তোমার স্থান এখন দ্বিতীয় সারিতে।
দ্বিতীয় সারি! প্রফেসর হেইসেনবের্গ জীবনে কোনো পরীক্ষায় কখনও দ্বিতীয় হননি। ম্লান হাসলেন তিনি। বললেন, ইয়েস প্রফেসর। সে কথা আর বলতে!
সহ্য হল না ওয়াইৎসেকার-এর। বললেন, না! আমেরিকান-বৈজ্ঞানিকদের কাছে নয়।
-নয়?
-না, প্রফেসর হান। আমরা হেরে গেছি হিটলারের ইহুদি-বিদ্বেষ নীতির কাছে। আমেরিকান কে? আইনস্টাইন, ম্যাক্স বর্ন, জেমস ফ্রাঙ্ক, নীলস বোহর? নাকি ৎজিলাৰ্ড, টেলার, ফের্মি, ফুস্, ওয়াইসকফ, কিস্টি, রবিননাভিচ? কে? কে আমেরিকান?
মাথা নেড়ে প্রফেসর হান বলেন, আমি জানি না–এ বোমা কে বানিয়েছে। আমি শুধু জানি, আমার অপরাজিত শিষ্য হেইসেনবের্গ আজ দ্বিতীয় সারিতে।
–আমি স্বীকার করছি, স্যার। মাথাটা নিচু করলেন হেইসেনবের্গ।
কিন্তু অত সহজে ওয়াইৎসেকার মেনে নিলেন না এ অভিযোগ। দৃঢ়স্বরে বললেন, আমি মানি না একথা। হিটলারের হাতে তুলে দেব না বলেই আমরা ওটা বানাইনি–না হলে ওদের আগে, অনেক-অনেক আগে ওটা তৈরি করতে পারতাম আমরা।
আহারান্তে রাত নয়টায় বিস্তারিত রেডিও বুলেটিন শুনলেন ওঁরা। তারপর একে একে যে যার বিছানায় চলে গেলেন। শুভ রাত্রি’ ঘোষণা করার কথা আজ আর কারও মনেও পড়ল না। হলের মধ্যে আটখানা খাট পাতা আর বয়োজ্যষ্ঠ দুজনের জন্য আছে একটি পৃথক ঘর। ফন লে আর অটো হানের ঘর। সকলেই শুয়ে পড়েছেন, কিন্তু ঘুম আসছে না কারও। হঠাৎ রাত দুটোর সময় প্রফেসর ফন লে এ ঘরে এসে বললেন–তোমরা একবার ও ঘরে চল। প্রফেসর হান যেন কেমন করছেন!
তড়াক করে লাফিয়ে ওঠেন হেইসেনবের্গ। কেমন করছেন মানে? কী করছেন?
–আমার আশঙ্কা হচ্ছে, উনি আত্মহত্যার কথা ভাবছেন।
ওঁরা ধীরপদে একে একে আসেন এ ঘরে। মোমবাতি জ্বলছে বন্দিশালায়। স্তিমিত আলোকে দেখা যায় খাটের ওপর চুপ করে বসে আছেন বৃদ্ধ। চোখে উদ্ভান্ত পাগলের দৃষ্টি। হেইসেনবের্গ সন্তর্পণে এগিয়ে আসেন। হাতটা তুলে নেন তাঁর। সম্বিত ফিরে পান বৃদ্ধ। বিহুলের মতো তাকিয়ে দেখেন পুত্রপ্রতিম শিষ্যের দিকে। হেইসেনবের্গ বললেন, স্থির হোন প্রফেসর! হেরে গেছি তাতে হয়েছেটা। কী? হারতেই কি চাননি এতদিন? আপনি নিজেই তো একদিন বলেছিলেন–হিটলারের হাতে অ্যাটম বোমা তুলে দেওয়ার আগে আত্মহত্যা করব আমি।
বৃদ্ধের ঠোঁট দুটি নড়ে ওঠে। অস্ফুটে বলেন, সেজন্য নয়, ওয়ার্নার, সে জন্য নয়।
–তবে কী জন্য?
–ঐ ম্যাথমেটিক্যাল ফিগারটা। হান্ড্রেড থাউজেন্ড। টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ।
-কিন্তু আপনি তার কী করবেন, স্যার? আপনি কেন এতটা ভেঙে পড়ছেন?
দু-হাতে মুখ ঢেকে বৃদ্ধ হাহাকারে ভেঙে পড়েন: আমি..আমিই যে ওদের প্রথম পথ দেখিয়েছিলাম মাই বয়!…আমার হাতটা আজ রক্তে লাল হয়ে গেছে…. দেখছ না! হান্ড্রেড থাউজেন্ড সোস্।
বলিরেখাঙ্কিত হাতটা বাড়িয়ে ধরেন মোমবাতির স্তিমিত আলোয়।
হেইসেনবের্গ ওঁর মাথাটা নিজের বুকের ওপর টেনে নেন। পাকা চুলে ভরা মাথার ওপর হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন। যেন বাচ্চা ছেলেকে ঘুম পাড়াচ্ছেন।
***
6.8.1945। বিজয়ী পৃথিবী আনন্দ-উৎসবে নাচছে। গোটা আমেরিকা আজ আলো-ঝকমল। কম-বেশি সবাই মাতাল। শুধু একটি লোক দৃঢ় পদবিক্ষেপে এগিয়ে আসছিল সান্তা-ফের কাছে, কাস্টিলো ব্রিজ স্টেশনের দক্ষিণতম প্রান্তে। জায়গাটা জনবিরল। লোকটার পরনে গ্রে রঙের স্যুট। মাথার টুপিটা নামানো, মুখে আলো পড়েনি। হাতে কিছু নেই। ঠোঁটে ঝুলছে সিগারেট। স্টেশনের শেষ প্রান্তে এখানটা আলো-আঁধারি। হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল লোকটা। দেশলাইয়ের শেষ কাঠিটা জ্বেলে নিবে যাওয়া সিগারেটটা ধরালো। সেই আলোয় মুখের একটা আভাস দেখা গেল।
হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে এগিয়ে এল আর একজন। বললে, পূর্বদিকে যাবার ট্রেন কখন পাওয়া যাবে বলতে পারেন?
লোকটা আগন্তুককে আপাদমস্তক দেখে নিল একবার। হা পোশাকের বর্ণনা নিখুঁত। যেমনটি হবার কথা। নীল স্যুট, সাদা-কালো ডোরাকাটা টাই, মাথায় বাউলার হ্যাট। তবু সন্দেহ ঘোচে না লোকটার। বলে, জানি না। কোথা থেকে আসছেন আপনি?
অতি নিম্নস্বরে লোকটা বলল; I come from Julius!
এতক্ষণে নিশ্চিত হওয়া গেল। শেকহ্যান্ড করল আগন্তুকের সঙ্গে। বললে, আমার নাম ডেক্সটার। আপনার?
–চার্লস রেমন্ড। হাউ ডু য়ু ডু?
ডেক্সটার বললে, কোথাও গিয়ে কিছু খেলে হত।
–আসুন। স্টেশনের কাছেই আমার জানা একটা ভালো রেস্তোরাঁ আছে।
দুজনে এগিয়ে গেল জনাকীর্ণ প্ল্যাটফর্ম দিয়ে। আর কোনো কথা হল না পথে। প্ল্যাটফর্ম টিকিট ছিল দুজনেরই। দাখিল করে বেরিয়ে এল রাস্তায়। অনতিদূরের এক পানাগারে ঢুকল দুজন। দূরের একটা আলো-আঁধারি কোণে গিয়ে বসল। তখনও দুজন নির্বাক। এতক্ষণে নজর হল ডেক্সটারের, চালর্স-এর হাতে রয়েছে। একটা অ্যাটাচি-কেস। কিন্তু ওর তো খালি হাতে আসার কথা।
ওয়েটার এসে দাঁড়ায়। দু-পেগ কনিয়াকের অর্ডার নিয়ে চলে গেল। ডেক্সটার সন্তর্পণে তার পকেট থেকে বার করে আনল একটা কাগজের টুকরো। নিঃশব্দে রাখল সেটা টেবিলের ওপর। কোনো একটা রেস্তোরাঁ-রসিদের একটা ছেঁড়া টুকরো। চালর্স নজর করলে দেখতে পেত রসিদটা ‘গোল্ডেন ড্রাগন’ পাব-এর মদের বিল। সানফ্রান্সিস্কোর একটি পানাগারের। তারিখটা চার মাস আগেকার। সে কিন্তু নজরই করল না এসব। সন্তর্পণে তার বাঁ-পকেট থেকে বার করল অনুরূপ একখণ্ড ছেঁড়া কাগজ। ডেক্সটার দুটো টুকরো পাশাপাশি জোড়া দিচ্ছিল যখন, তখন চার্লস নজর রাখছিল চারদিকে। না, কেউ লক্ষ্য করছে না ওদের। দুটি ছেঁড়া কাগজ খাঁজে খাঁজে মিলে গেল। কুচিকুচি করে কাগজটা ডেক্সটার ফেলে দিল অ্যাশট্রেতে।
ওয়েটার এসে দাঁড়াল। নামিয়ে রাখল দুটি পানপাত্র। হলুদ রংএর পানীয়। পরস্পরের স্বাস্থ্য পান করল ওরা নীরবে।
এরপর ডেক্সটার তার পকেট থেকে বার করল একটা পলমল সিগারেটের প্যাকেট। প্যাকেট থেকে সিগারেট বার করল না কিন্তু। গোটা প্যাকেটটাই চার্লস-এর দিকে বাড়িয়ে ধরে বললে, গট ম্যাচেস্?
-ইয়াহ!
চার্লস গ্রহণ করল সিগারেটের গোটা প্যাকেটটা। মুষ্টিবদ্ধ হাতটা ঢুকিয়ে দিল পকেটে। পরমুহূর্তেই হাতটা বার করে আনল। তাতে পলমলের প্যাকেটটা তো আছেই, আছে একটা লাইটারও। দুজনে দুটো সিগারেট বার করে ধরালো। ডেক্সটার এবার সিগারেটের প্যাকেটটা নিয়ে নিজের পকেটে রাখল। যার সিগারেট তার পকেটেই ফিরে গেল।
ইতিমধ্যে ঠিক ওদের পাশের টেবিলে এসে বসেছে একটি ছেলে আর মেয়ে। তাদের চোখের সামনেই ঘটল ব্যাপারটা। মেয়েটা কেমন যেন ওদের দিকে তাকাচ্ছে বারে বারে। চার্লস অস্বস্তি বোধ করছে। ইঙ্গিত করল সে বন্ধুকে। দুজনে উঠে পড়ল। অতি দ্রুতচ্ছন্দে গ্লাস দুটো শেষ করে।
ওয়েটার এসে দাঁড়াল। দাম মিটিয়ে দিল চার্লস।
ম্লান হাসল ডেক্সটার। কী আশ্চর্য! চার্লস লোকটাকে টিপস্ দিল বিলের মাত্র শতকরা দশের হিসাবে। কী কৃপণ লোকটা! ভাবছিল ডেক্সটার। আর কেউ না জানলেও ওরা দুজন এবং রেমন্ডের ডান-পকেটের ইনসাইড লাইনিংটা তো জানে, সিগারেট প্যাকেটের বদল হয়ে গেছে। লোকটার পকেটে এখন যে প্যাকেটটা আছে তার দাম মিলিয়ান নয়– বিলিয়ন ডলারের হিসাবে।
কিন্তু উপায় ছিল না চার্লস-এর। সে কত টিপস্ দেবে তারও নির্দেশ সে পেয়েছিল। টিপসের অঙ্কটা যেন এতবেশি না হয় যাতে ওয়েটারটা কৃতজ্ঞ হয়ে দ্বিতীয়বার ওর মুখের দিকে তাকায়। আবার এত কমও যেন না হয়, যাতে অন্য কারণে সে চোখ তুলে তাকায়।
পথে নেমে এসে ডেক্সটার বলল, গুড নাইট!
–জাস্ট এ মিনিট। তোমার অ্যাটাচি-কেসটা ফেলে যাচ্ছ।
হাত বাড়িয়ে অ্যাটাচি-কেসটা চার্লস দিতে চায় ডেক্সটারকে। ভ্রূদুটি কুঞ্চিত হয়ে ওঠে ডেক্সটারের। বলে, কী আছে ওতে?
চারদিকে চোখ বুলিয়ে একবার দেখল চার্লস। রাস্তার এদিকটা এখন জনশূন্য। নিম্নকণ্ঠে বললে, ওজনটা তুমিই দেখ। অল ইন টোয়েন্টি অ্যান্ড ফিফটি ডলার বিলস্।
অর্থাৎ বিশ এবং পঞ্চাশ ডলারের খুচরো নোট। যা অপরাধ-বিজ্ঞানের ভাষায় ‘নম্বরী নোট’ নয়। যা সহজে খরচ করা যাবে। ডেক্সটার একজন বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী। সুটকেসের ওজনটা বাদ দিয়ে “নেট ওজনে’ ডলারের অঙ্কটা টেন-টু-দ্য-পাওয়ার কততে দাঁড়াবে আন্দাজ করতে তার কোনো স্লাইড-রুলের প্রয়োজন হল না। বললে, এ শর্ত ছিল না তো
–জুলিয়াস বিনা পারিশ্রমিকে কাউকে দিয়ে কোনো কাজ করায় না।
হঠাৎ ধক করে জ্বলে উঠল ডেক্সটারের চোখ দুটো। বললে, দেন গিভ মি ব্যাক মাই সিগারেট-প্যাকেট!
আঁতকে ওঠে রেমন্ড: কী ব্যাপার?
-জুলিয়াসকে বোলো-ডেক্সটার অর্থের লোভে একাজ করছে না।
–ঠিক হ্যায়।
কোনোরকম বিদায় সম্ভাষণ না জানিয়েই চার্লস অ্যাটাচিটা হাতে হাঁটতে শুরু করে। একটা ট্যাক্সি আসছিল এদিকে। সেটাকে দাঁড় করায়। পালাতে পারলে সে বাঁচে।
ডেক্সটার অন্যমনস্কর মতো হাঁটতে থাকে ফুটপাথ ধরে।
সেই রাত্রে লস অ্যালামসে ফিরে ডেক্সটার শোওয়ার আগে দিনপঞ্জিকায় লিখেছিল:
Others talk, hope, wait and are repeatedly disappointed, be cause they don’t understand the true nature of political power. Well, I’m going to act. I’ve acted. May be I have prevented another World War.
: ওরা বাকবিস্তার করে, আশা করে, অপেক্ষা করে আর বারে বারে বোকা হয়, কারণ ওরা জানে না রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রকৃত স্বরূপ। আমি ও ফাঁদে পা দেব না। যা করবার নিজেই করব। করেছি। হয়তো আজ আমিই পথ রুদ্ধ করে দিয়ে। গেলাম তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের।
তারপর বাতি নিবিয়ে শুয়ে পড়ল।
তবু শেষ হল না দিনটা। মিনিটদশেক বিছানায় পরে থেকে আবার উঠল। আলোটা জ্বালল। দিনপঞ্জিকার পাতাখানা পড়ল আবার। হাসল। ছিঁড়ে নিল পাতাটা। তারপর দেশলাই জ্বেলে লেখাটা পুড়িয়ে ছাই করে দিল।
পাঠকের হয়তো স্মরণ আছে-আমি অনেক আগেই বলেছি–এ বিশ্বাসঘাতকতার মূল্যায়ন করতে বসে একটা সমীকরণ কষে দুটি ফল পেয়েছি। একটা বিলিয়ন ডলারের অঙ্ক এবং দ্বিতীয়টা শূন্য।
আশা করি হিসাবের কড়ি বাঘে খায়নি।
x(x –10^9) = 0
ইকোয়েশানের দুটি ‘রূপ’ই নির্ভুল। এ বিশ্বাসঘাতকতার মূল্যমান বিলিয়ান ডলারেও প্রকাশ করা যায়; আবার বলা যায়, সেটা স্রেফ শূন্য! কিউ. ই. ডি.।
৬. কেন ১-৪
০১.
তিমি-শিকারী দলটাকে পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হল। হ্যাঁ, ‘তিমি-শিকারীর দল। যুগ্মসচিবের নির্দেশ নিয়ে এফ. বি. আই. চিফের কাছে যখন অনুসন্ধানের আদেশ এল তখন তৈরি হল এই ‘হোয়েলার্স–স্কোয়াড। তিমি-শিকারীরা হারপুন দিয়ে বিঁধে আনবে সেই অতলসঞ্চারী তিমি মাছটিকে–ডেক্সটার! একা ডেক্সটার নয়, ইতিমধ্যে জানা গেছে, আরও দুজন ছোট-মাপের বিশ্বাসঘাতক এই দুষ্কার্যে প্রত্যক্ষ অংশ নিয়েছে। তাদের ছদ্মনাম যথাক্রমে ‘অ্যালেক্স’ আর ‘ডগলাস’। এফ. বি. আই. অনুসন্ধান করে বুঝেছে–ওই তিনজন পৃথক পৃথকভাবে গুপ্তচরবৃত্তিতে অংশ নিয়েছে, তারা সম্ভবত পরস্পরকে চেনে না। মানে স্বনামে হয়তো চেনে–গুপ্তচর হিসাবে ছদ্মনামে চেনে না। আরও জানা গেছে, সর্বনাশের সিংহভাগ দাবী করতে পারে একমাত্র ডেক্সটার একাই। অ্যালেক্স এবং ডগলাস মিলিতভাবে যদি চার-আনা ক্ষতি করে থাকে, তবে ডেক্সটার একাই করেছে বারো আনা।
খুব ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে হবে। রাতারাতি রাঘববোয়াল জালে ধরা পড়বে না! প্রথমে চিহ্নিত করতে হবে ওই দুটি চুনোপুঁটিকে : অ্যালেক্স এবং উল্লাস। তাদের স্বীকারোক্তি থেকেই হয়তো পাওয়া যাবে ডেক্সটার-বধের ব্রহ্মাস্ত্র।
যুদ্ধসচিবের নির্দেশ পাওয়ার পর কর্নেল ল্যান্সডেল মূল পরিকল্পনাটা ছকে ফেলেছেন। কর্নেল প্যাশকে নিজের চেম্বারে ডেকে নিয়ে তিনি পরিকল্পনাটা বুঝিয়ে দিলেন
হোয়েলার্স-স্কোয়াডে থাকবে পাঁচটি ইউনিট। পাঁচটি বিভাগের পাঁচজন দলপতি থাকবেন। বিভাগের নামগুলি মূলত দেশ অনুসারে।
হাঙ্গেরিয়ান-য়ুনিট অনুসন্ধান করবেন তিনজন বিজ্ঞানীর বিষয়ে, তারা হলেন ফন নয়ম্যান, ৎজিলাৰ্ড এবং টেলার। এর মধ্যে মূল লক্ষ্য হলেন ৎজিলাৰ্ড। তিনি বরাবর অ্যাটম-বোমা নিক্ষেপের বিরুদ্ধে কাজ করে গিয়েছেন। গোপনীয়তার নির্দেশ অমান্য করে লস-অ্যালামসের বৈজ্ঞানিকদের ভিতর প্রচার-পুস্তিকা বণ্টন করেছেন–বোমা-বিরোধী ফ্রন্ট গঠনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন।
দ্বিতীয় বিভাগ হচ্ছে রাশিয়ান-য়ুনিট। তার মূল লক্ষ্য ক্রিস্টিয়াকৌস্কি। রোবিনোভিচ অবশ্য বোমা-নিক্ষেপের বিরুদ্ধে দল ও মত গঠনে সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন; কিন্তু গুপ্তচরবৃত্তি যেন তার চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। তা হোক–খবরটা পাচার হয়েছে রাশিয়ায়। ফলে দুজন রাশিয়ান বৈজ্ঞানিককেই যাচাই করে দেখতে হবে।
তৃতীয় অনুসন্ধানী দল পরীক্ষা করবে অপর চারজন বৈজ্ঞানিককে। এই দলের কার্যপ্রণালী উপবৃত্তের আকার নেবে। কেন্দ্র একটা নয়; দু-দুটো। উপবৃত্তের এক কেন্দ্র ডি ফাইনম্যান-সেই আপাত-ছেলেমানুষ দুর্ধর্ষ প্রতিভাবান ব্যক্তিটি, এবং দ্বিতীয় কেন্দ্র অটো কার্ল।
চতুর্থ দল যাচাই করবে ভিক্টর ওয়াইস্কফ আর এনরিকো ফের্মিকে। প্রফেসর নীলস বোহরকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তার মতো অন্যমনস্ক মানুষের পক্ষে কোনো ষড়যন্ত্রে অংশ নেওয়া একেবারেই অসম্ভব।
পঞ্চম দলের লক্ষ্য একমাত্র একজন বৈজ্ঞানিক : রবার্ট জে ওপেনহাইমার।
কর্নেল ল্যান্সডেলের বিশ্বাস ‘ডেক্সটার’ একা নয়, অ্যালেক্স এবং ডাসকেও এই পাঁচটি দলের অন্তর্ভুক্ত এই বারোজনের সন্ধানকালেই হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে, হয়তো উপগ্রহ হিসাবে। কর্ণেল প্যাশকে তিনি বললেন, পাঁচটি যুনিটের জন্য পাঁচজন দলপতিকে এখনই নির্বাচিত করতে হবে, এবং তুমি থাকবে এই পাঁচজনের শীর্ষস্থানে, যোগাযোগ-রক্ষাকারী হিসাবে।
কর্নেল প্যাশ জবাবে সবিনয়ে বললেন, স্যার, আপনি যদি অনুমতি করেন তবে আমি একটি বিকল্প প্রস্তাব রাখতে চাই।
–বল।
–আপনি নিজেই এই পাঁচটি দলের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হয়ে হোয়েলার্স-স্কোয়াড’ পরিচালনা করুন। আমি ওই পাঁচটি দলের একটি বিশেষ দলের দলপতি হতে চাই।
-কেন? কোন্ দলের?
–পঞ্চম দলের। আমি ওই ডক্টর ওপেনহাইমারের কেসটার তদন্তভার নিতে চাই।
কর্নেল ল্যান্সডেল নীরবে কিছুক্ষণ ধূমপান করেন। তারপর বলেন, ও. কে.। তাই হোক। এবার বাকি চারটি দলপতি কাকে কাকে করতে চাও বল?
-আমার মনে হয় তৃতীয় দলটিকেও আপনি দুভাগ করুন। তার কারণ প্রফেসর অটো কার্ল শীঘ্রই ইংল্যান্ডে ফিরে যাচ্ছেন, অথচ প্রফেসর ফাইনম্যান কলোম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি নিয়েছেন। একজন গোয়েন্দার পক্ষে পৃথিবীর দু প্রান্তে
-কারেক্ট। তাহলে আমাদের পাঁচজন লোকের প্রয়োজন।
প্রফেসর ফাইনম্যানের পেছনে লেগে থাকবে ম্যাককিলভি–যে ছিল লস অ্যালামসে আমাদের সিকিউরিটি অফিসর। ম্যাককিলভি আমাকে জানিয়েছে যে, ইতিমধ্যেই প্রফেসর ফাইনম্যানের বিরুদ্ধে কিছু গোপন তথ্য সংগ্রহ করেছে। ব্যাপারটা কী তা সে বলেনি, ওর মতে আরও একটু নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগৃহীত না হলে সে রিপোর্টটা দিতে পারছে না। ভাবছি, ম্যাককিলভিকে কলোম্বিয়ায় বদলি করে দেব। দ্বিতীয়ত, প্রফেসর অটো কার্ল-এর বিরুদ্ধে নিযুক্ত করতে চাই উইলিয়াম জেমস্ স্কার্ডনকে। ছোকরা আমেরিকান নয়, ব্রিটিশ-বর্তমানে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডে নিযুক্ত আছে। আমার সঙ্গে দীর্ঘদিনের আলাপ। আপনি অনুরোধ জানালে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড স্কার্ডনকে হারওয়েলে বদলি করবে।
–হারওয়েল কোথায়? সেখানে কেন?
–হারওয়েল অক্সফোর্ডের কাছাকাছি একটা আধা-শহর। সেখানে একটা নিউক্লিয়ার ল্যাবরেটরি তৈরি হচ্ছে। পারমাণবিক-শক্তিকে যুদ্ধোত্তরকালে মানবকল্যাণে লাগানো যায় কিনা গ্রেট ব্রিটেন তাই দেখতে চায় হারওয়েলে। প্রফেসর অটো কার্ল সেই প্রকল্পে একটা চাকরি নিয়ে যাচ্ছেন। স্যার জন কক্ৰক্ট-এর অধীনে। ক্লাউস ফুকসও যাচ্ছেন সেখানে।
***
লস অ্যালামসে তখন ভাঙা হাট। শিবির ভাঙার পালা। অথবা বলা যায় ফুলশয্যা-বৌভাত মিটে যাবার পর বিয়েবাড়ির অবস্থা। দেশ-বিদেশ থেকে বরযাত্রীরা এসে জুটেছিল নিমন্ত্রণ পেয়ে। শুভকাজ নির্বিঘ্নে মিটে গেছে। পরের ঘরের মেয়ে এ বাড়িতে নববধূ হয়ে ঘোমটা টেনে বসেছে অন্দরমহনের গোপন একান্তে। এবার বরযাত্রীরা যে যার ডেরায় ফিরে যাবে। বিজ্ঞানীর দল প্রতিদিনই নতুন নতুন চাকরির নিয়োগপত্র পাচ্ছেন। ঘরোয়া বিদায়পর্ব লেগেই আছে। যুদ্ধজয়ের মাত্র দু-মাসের মধ্যে ওপেনহাইমার পদত্যাগ করলেন। কার্যভাব বুঝে নিলেন ব্র্যাডলি। ওপেনহাইমার তখন জাতীয় বীর। প্রথম মাসখানেক অভিনন্দন-সভায় উপস্থিত থাকাই ছিল তার একমাত্র কাজ। টের হাইড্রোজেন-বোমা আবিষ্কারের নতুন প্রকল্প নিয়ে মেতেছেন। ৎজিলাৰ্ড বিরক্ত হয়ে ফিরে এসেছেন এ নারকীয় মারণযজ্ঞ থেকে। অটো কার্ল আর ক্লাউস ফুৰ স্ ফিরে যাচ্ছেন ইংল্যান্ডেহারওয়েল-এ এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে, পারমাণবিক-শক্তিকে মানব কল্যাণে ব্যবহার করা যায় কিনা তাই পরীক্ষা করে দেখতে।
মার্কিন কর্মকর্তারা এতদিনে পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ভেবে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। ভুল বললাম, পৃথিবীর নয়, আমেরিকার। রাশিয়ার সঙ্গে একটা চুক্তিবদ্ধ হলে ভালো হয়। ওঁদের বক্তব্য : হে বন্ধু, তোমাদের অ্যাটম-বোমা নেই, আমাদের আছে–তবু বিশ্বশান্তির মুখ চেয়ে আমরা নিজে থেকেই প্রস্তাব তুলছি; এস, একটা ভদ্রলোকের চুক্তি করা যাক–আমরা দুজন কেউ কারও ওপর অ্যাটম-বোমা ঝাড়ব না।
1945 সালে মস্কোতে হল একটি মহাসম্মেলন–চতুঃশক্তির শীর্ষ বৈঠক। ফোর-পাওয়ার কনফারেন্স। অথচ কিমাশ্চর্যমতঃপরম। যাদের এ-বিষয়ে সবচেয়ে উৎসাহিত হবার কথা, তারাই ধামা চাপা দিল প্রস্তাবটা। রাশিয়ার ডেলিগেট মলোটভ বললেন, আপাতত ও আলোচনাটা মুলতুবি থাক। পরবর্তী অধিবেশনে এটা নিয়ে আলোচনা করা যাবে বরং।
আমেরিকা এটা আদৌ প্রত্যাশা করেনি। মলোটভের ঔদাসীন্যের কোনো হেতুই সেদিন বোঝা গেল না।
সেটা বোঝা গেল আরও চার বছর পর। 1949-এর অগাস্ট মাসে একটি মার্কিন বি-29 বিমান কতকগুলি ফটো দাখিল করল। ওয়াশিংটনের বিশেষজ্ঞরা সেই ফটো পরীক্ষা করে বুঝলেন, সাইবেরিয়ার কোনো নির্জন অঞ্চলে রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। তাই ফটো-প্লেটে রেডিও-অ্যাকটিভিটির দাগ পড়েছে! অর্থাৎ পাল্লা এতদিনে সমান-সমান হয়েছে। এতদিনে বোঝা গেল, পটসড্যামে স্তালিন এবং মস্কো সম্মেলনে মলোটভ কেন অমন ঔদাসীন্য দেখিয়েছিলেন। কিন্তু রাশিয়ায় তো ইউরেনিয়াম নেই। কেমন করে পরমাণু-বোমা বানালো ওরা?
তখন ওরা তা বুঝতে পারেননি। ৎজিলাৰ্ডকে তো বার্জে ঠাট্টা করে একদিন বলেই ছিলেন, ফর্মুলাটা পেলেও রাশিয়া কোনোদিন অ্যাটম বোমা বানাতে পারবে না। তার ভাঁড়ারে ইউরেনিয়াম নেই। আজ এ গ্রন্থ রচনাকালে পৃথিবী অবশ্য জানতে পেরেছে এ ধাঁধার সমাধান। রাশিয়ান জিওলজিস্ট বিখ্যাত পণ্ডিত ভরনাভস্কি মহান নেতা লেনিনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার অবকাশে এ ধাঁধার সমাধানটা ঘটনাচক্রে জানিয়ে দিয়েছেন আমাদের। ভরনাভস্কি বলেছেন, 1921 সালেই লেনিন তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন রাশিয়ায় প্রত্যেকটি প্রত্যন্ত দেশে যেসব খনিজ সম্পদ আছে তার বিধিবদ্ধ অনুসন্ধান চালাতে। ওঁরা অর্থাৎ ভূতত্ত্ববিদেরা ইউরেনিয়ামের সন্ধান পেয়েছিলেন। বস্তুত লেনিন জীবিত থাকতেই (1870 1924) সোভিয়েত রাশিয়ার পাঁচ-পাঁচটি কেন্দ্রে নিউক্লিয়ার রিসার্চের কাজ শুরু হয়ে যায়। এই চারটি কেন্দ্র হল–লেনিনগ্রাডের রেডিয়াম ইন্সটিটুট এবং ফিজিক্স ইন্সটিটুট আর মক্সোর লেবেডফ ইন্সটিটুট এবং ইন্সটিটুট ফর ফিজিকাল প্রবলেম। পঞ্চম প্রতিষ্ঠানটি ছিল খারখভে অবস্থিত। অটো হানের আবিষ্কারের ঠিক পরেই রাশিয়ার শিক্ষামন্ত্রী–বৈজ্ঞানিক কাফতান-বার্লিনে এসেছিলেন। অটো হানের বিজ্ঞানাগার তিনি খুঁটিয়ে দেখেন এবং অটো হানকে নানান প্রশ্ন করে ব্যাপারটা জেনে নেন। তখনও, সেই 1939-এও, এটাকে গোপন তথ্য বলে কেউ মনে করত না। লেনিনের দূরদর্শিতা, রাশিয়ার মূল-ভূখণ্ডে ইউরেনিয়াম আবিষ্কার, এবং ওদের এতদিনের সাধনার কথা লৌহ-যবনিকার এপারে কেউ জানত না। প্রথম জানল ওই বি-29 প্লেনের রিপোর্ট পেয়ে, সাইবেরিয়ার আকাশে অ্যাটম-বোমা বিস্ফোরণের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়ার পর।
***
কিন্তু সেসব কথা তো অনেক পরের। আগের কথা আগে বলি।
দুসপ্তাহের মধ্যেই কর্নেল প্যাশ এসে রিপোর্ট করল কর্নেল ল্যান্সডেলের কাছে : স্যার, জাল ক্রমশ ছোটো হয়ে আসছে। আপনার নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ-পাঁচটি টিমই কাজে লেগে গিয়েছে; কিন্তু আমার দৃঢ় ধারণা হচ্ছে তিনজনের মধ্যেই মূল অপরাধীকে খুঁজে পাওয়া যাবে।
-কোন তিনজন?
–ডিক ফাইনম্যান, ওপেনহাইমার অথবা অটো কার্ল।
কর্নেল ল্যান্সডেল বলেন, ফাইনম্যান আর ওপেনহাইমার সম্বন্ধে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। ওঁদের দুজনের মধ্যে একজন যদি ডেক্সটার হন আমি বিস্মিত হব না। কিন্তু আমার এক মাসের বেতন এক বোতল হুইস্কির বিনিময়ে তোমার সঙ্গে বাজি রাখতে রাজি আছি, অটো কার্ল এর ভেতর নেই।
কৌতুক উপচে পড়ল প্যাশের দু-চোখে। বলল, স্যার, আপনার গোটা মাসের মাইনেটা এভাবে হাতিয়ে নিতে আমার বিবেকে বাধছে। যা হোক, এত বড় কথাটা কেন বললেন?
–অটো কার্ল-এর ‘অ্যালেবাই’টা আমি যাচাই করে দেখেছি। নিখুঁত, নীর। পাঁচই অগাস্ট প্রফেসর কার্ল সান্তা ফে থেকে প্লেনে চড়েন। ছয়ই সমস্তটা দিন তিনি ছিলেন নিউইয়র্কে। ছয়ই তারিখ সন্ধ্যায় তিনি স্বয়ং জেনারেল গ্রোভসসের সঙ্গে কথা বলছিলেন।
–সো হোয়াট?
-কী আশ্চর্য। তুমি ভুলে গেছ প্যাশডেক্সটার ছয়ই অগাস্ট রাত্রে সান্তা ফে-র একটা আসবাগারে মাইক্রোফিল্মটি হস্তান্তরিত করে। যেহেতু ওই সময়ে প্রফেসর কার্ল সান্তা ফে থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে ওয়াশিংটনে ছিলেন তার অকাট্য প্রমাণ রয়েছে–
বাধা দিয়ে প্যাশ বলে, স্যার! ও ‘অ্যালেবাই’টা আমিও যাচাই করে দেখেছি। শুধু তাই নয়, প্রফেসর কার্লের হঠাৎ ওয়াশিংটনে আসার কোনো জোরালো যুক্তি আমি খুঁজে পাইনি–একমাত্র যুক্তি ওই ‘অ্যালেবাই’ প্রতিষ্ঠা করা। তা থেকেই আমার মনে হয়েছে
কর্নেল ল্যান্সডেল বাধা দিয়ে বলেন, তুমি পাগল না আমি পাগল বুঝে উঠতে পারছি না। কার্ল কেমন করে একই সময়ে কয়েক হাজার মাইল দূরত্বে….
–তাহলে আমার ইনভেস্টিগেশন রিপোর্টটা বিস্তারিত শুনুন
ধুরন্ধর গোয়েন্দা কর্নেল প্যাশ। প্রতিটি পদক্ষেপ তার নিখুঁত। ছয়ই অগাস্ট কার কার ‘অ্যালেবাই’ আছে প্রথমেই সে সেটা যাচাই করে দেখে নেয়। ফাইনম্যানের। নেই, ওপেনহাইমারের নেই, ৎজিলার্ডের নেই। আছে যাদের তারা হলেন–ফন নয়ম্যান, ম্যাক্স বর্ন, ক্লাউস ফুকস, অটো কার্ল প্রভৃতির। নয়ম্যান লস অ্যালামসে ছিলেন, ম্যাক্স বর্ন রুদ্ধদ্বার কক্ষে সস্ত্রীক উপস্থিত ছিলেন, ক্লাউস ফুকস্ এদিন রাত্রে সবাইকে প্রচুর মদ এনে খাওয়ায়। মদের আসরে অধিকাংশই অংশগ্রহণ করেন। একমাত্র ৎজিলাৰ্ড ও ফাইনম্যান জাপানে বোমাবর্ষণের জন্য কোনো আনন্দ উৎসবে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। তারা দুজনে ভোজনাগার ছেড়ে চলে যান। বাকি রাত তারা কোথায় কাটান তা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না। আর অটো কার্ল আগের দিন থেকে ওয়াশিংটনে ছিলেন।
ফলে অ্যালেবাই-এর হিসাব অনুসারে তিনটি নাম লিপিবদ্ধ হল প্যাশ-এর ডায়েরিতে। ফাইনম্যান, ওপেনহাইমার এবং ৎজিলাৰ্ড।
***
দ্বিতীয় পর্যায়ের অনুসন্ধান প্যাশ শুরু করে অন্যদিক থেকে। ফটো তোলার। বাতিক কার আছে। মাইক্রোফিল্ম তৈরি করবার মতো উপযুক্ত যন্ত্র কার কাছে থাকতে পারে? এই সূত্র ধরে একটা অদ্ভুত তথ্য পেয়ে গেলো। ওর প্রথমেই মনে হল, লস অ্যালামসে ফটো-ডিলার কে কে খোঁজ করতে হবে। তার কাছেই সন্ধান পাওয়া যাবে কে কে তার গ্রাহক, ফটোগ্রাফির বাতিক আছে কার কার। কথাপ্রসঙ্গে সে ক্লাউস ফুকসকে প্রশ্ন করল, ‘আই সে ডক্টর, লস অ্যালামসে কোনো ফটোগ্রাফারের দোকান আছে? কিছু ফটো তুলেছি, ডেভেলপ করতে দিতাম।
ক্লাউস ফুকস্ জবাবে বলেন, লস অ্যালামসে কোনো ফটোগ্রাফার নেই। সান্তা ফে-তে পাবেন। তবে তাড়াতাড়ি থাকলে আপনি প্রফেসর কার্ল-এর দ্বারস্থ হতে পারেন। ওঁর ফটোগ্রাফিতে ভীষণ ঝোঁক। নিজস্ব ডার্করুম আছে : সব কিছু নিজ হাতে করেন।
প্যাশ নির্বিকারভাবে বললে, না, শৌখিন ফটোগ্রাফার দিয়ে চলবে না। আমি যেটা ডেভেলপ করাতে চাই তা হচ্ছে মাইক্রোফিল্ম।
হা, হা তার ব্যবস্থাও আছে। প্রফেসর কার্ল ছাত্রজীবন থেকেই ওই মাইক্রোফিলম ব্যবহার করছেন। লাইব্রেরিতে বসে উনি নাকি কখনও লঙহ্যান্ডে নোট নেননি। পটাপট ছবি তুলে নিয়ে চলে আসতেন।
এবারও নির্বিকার ভাবে প্যাশ বলে, তাই নাকি। তবে তো ভালই। ওঁর কাছেই যাই
–কিন্তু প্রফেসর বোধ হয় কাল সানফ্রান্সিস্কো গেছেন। দাঁড়ান, জেনে নেই
ফুকস্ একটি ফোন করলেন। ও প্রান্তে ধরলেন ফ্রাউ কার্ল। শোনা গেল, ফুকসের অনুমানই সত্য। প্রফেসর তার ডেরায় নেই।
প্যাশ বলে–এখানে আর কেউ নেই যে ওঁর ডার্করুমটা ব্যবহার করে এটা ডেভেলপ করে দিতে পারে? আপনি পারেন?
–সর্বনাশ! আমি ফটোগ্রাফির কিছুই জানি না। আমার ক্যামেরাই নেই। আর তাছাড়া তেমন ফটোগ্রাফি-বিশারদ পেলেও কাজ হবে না। আমি নিশ্চিত জানি, প্রফেসর ওঁর ডার্করুম তালাবন্ধ করে গিয়েছেন। কাউকে ব্যবহার করতে দেন না সেটা। ওই ডার্করুমটা ওঁর প্রাণ। কাউকে ঢুকতেই দেন না সে ঘরে।
কর্নেল প্যাশ তখন মনে মনে দুইয়ে-দুইয়ে-চার করছে। অটো কার্ল জার্মান। তার ইংরেজি উচ্চারণ বিদেশির মতো। তিনি মাইক্রোফিল্ম তৈরি করতে পারেন। যন্ত্র নিজস্ব। ডেভেলপ করেন নিজে। ডার্করুমটা তার প্রাণ। কাউকে ঢুকতে দেন না। বাড়ির বাইরে গেলে সেটা তালাবন্ধ থাকে।
ফুকস্ আন্দাজ করতে পারে না, প্যাশের মনে তখন ঝড় উঠেছে। সে তখনও খোশগল্প চালায়। বলে, অদ্ভুত ফটো-তোলার হাত ভদ্রলোকের। বিশেষ করে ট্রিক-ফটোগ্রাফি। আমি তো ওঁর সহকারী হিসাবে পাঁচ বছর কাজ করছি, দেখেছি কী চমৎকার…আচ্ছা দাঁড়ান, ওঁর তোলা একটি ট্রিক-ফটোগ্রাফ আপনাকে দেখাই
আলমারি খুলে একটি ফটো বার করে আনে। পোস্টকার্ড সাইজ। ছবির ক্যাপশন, ‘হোয়েন কার্ল কনগ্রাচুলেটস কার্ল’। প্রফেসর কার্ল এটা ফুকসকে উপহার দিয়েছিলেন।
আশ্চর্য ছবিটা। প্রফেসর কার্ল নিজেই নিজের করমর্দন করছেন। অর্থাৎ দুপাশেই অটো কার্ল। ফুকস্ বললে, কী একটা পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত হওয়ায় কার্ল নাকি এই ফটোটা তোলেন। তিনি নিজেই নিজেকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। আমি তো আজও ভেবে পাই না, কেমন করে এটা ভোলা গেল–
–সুপার-ইম্পোজিশন! দু দিকে দাঁড়িয়ে দুখানা সেলফ-ফটো নিয়েছিলেন প্রথমে, তারপর প্রিন্ট করার সময়–জাস্ট এ মিনিট…
মাঝপথেই থেমে যায় প্যাশ। পকেট থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা বার করে গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে দু-তিন মিনিট পরীক্ষা করে ছবিটা। তারপর বলে, আশ্চর্য!
–আশ্চর্য নয়?
–না, সেজন্য নয়। আমি যে ব্যাখ্যা দিচ্ছিলাম তা ঠিক নয়। এ ছবি ‘সুপার-ইম্পোজিশন’ নয়। মানে দুবার ফটো তুলে একটি প্রিন্ট বানানো হয়নি। একবারই স্ন্যাপ হয়েছে।
-কেমন করে বুঝলেন?
প্যাশ হেসে বলেন, ডক্টর! এটা নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নয়। কেমন করে আপনাকে বোঝাবো? ফটোগ্রাফি হচ্ছে ক্রিমিনোলজির একটি বিশেষ শাখা। এই গ্রেনগুলো লক্ষ্য করুন…ওয়েল, এককথায় এটা সুপার-ইম্পোজিশন আদৌ নয়।
–কী জানি মশাই, আমি ওসব বুঝি না।
একটু ইতস্তত করে প্যাশ বলে, আচ্ছা ফ্রাউ কার্লকে আপনি চেনেন?
–ঘনিষ্ঠভাবে। প্রফেসর কার্লের সহকারী হিসাবেই শুধু নয়, তার বিবাহ যুগ থেকে। কেন?
–আপনি ওঁকে আর একবার ফোন করুন। আমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব। আপনিও আসুন না? অসুবিধা আছে?
-কিছু না। ফ্রাউ কার্ল আমার বান্ধবী পর্যায়ের। তার সান্নিধ্যে আধঘণ্টা সময় কাটাতে পারলে খুশিই হব আমি।
***
ফ্রাউ কার্ল অতি সুন্দরী। বয়স বছর ত্রিশেক। প্রফেসর কার্ল-এর চেয়ে অন্তত কুড়ি বছরের ছোটো। নিষ্ঠাবতী ক্রিশ্চান। কোয়েকার। জন্ম ভিয়েনায়-বাল্যকাল কেটেছে জার্মানিতে। ক্লাউস ফুকস-এর পিতা ডক্টর প্যাস্টর ফুকসের মন্ত্রশিষ্যা। ক্লাউস ফুকস-এর পিতৃদেব প্যাস্টর ফুকস্ ছিলেন তার আমলে একজন বিখ্যাত জার্মান কোয়েকার। বিশ্বভ্রাতৃত্বের পূজারী। নাৎসিদের হাতে নিগৃহীত হয়েছিলেন–জেল খেটেছেন, কিন্তু জার্মানি ত্যাগ করে যেতে অস্বীকার করেন। ফ্রাই রোনাটা কার্ল তার আদর্শে এই বিশ্বভ্রাতৃত্বে অনুপ্রাণিত, সেই সূত্রেই ক্লাউস ফুকস-এর সঙ্গে তার আলাপ। ছিপছিপে একহারা চেহারা, সাদা ধপধপে প্ল্যাটিনাম ব্লন্ড চুলের গোছা লুটিয়ে পড়েছে কাঁধের ওপর, যৌবন অটুট। এক সন্তানের জননী। সন্তানটি মারা গিয়েছে, অথচ দেখলে মনে হয় অবিবাহিতা তরুণী।
ওদের সমাদর করে বসালেন ফ্রাউ কার্ল। শ্যাম্পেন বার করে আনলেন। ফুকে ধমক দিলেন, আজকাল তো এ পাড়া মাড়াতেই দেখি না।
আর এ পাড়ায় আসব কী করতে? দরকার ছিল প্রফেসরের সঙ্গে অ্যাটম-বোমার জন্য। সে দরকার তো মিটেই গেছে।
–ও! অর্থাৎ আমার সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই। কেমন তো? অকৃতজ্ঞ কোথাকার! একদিন তোমার বিছানা সাফা করা থেকে ঘরদোর পরিষ্কার করা সবকিছু আমাকে দিয়ে করাওনি?
নিশ্চয়ই না। তুমি নিজের গরজে ওগুলো করতে।
–নিজের গরজ! কী গরজ ছিল আমার?
–তোমার ফিগার ঠিক রাখতে।
প্যাশ বাধা দিয়ে বলে ওঠে–প্লিজ, মিসেস কার্ল। তৃতীয় ব্যক্তির সামনে এভাবে হাটে হাঁড়ি ভাঙবেন না।
রাঙিয়ে ওঠে রোনাটা। হাত দিয়ে মাথার চুলগুলো পিছনে সরিয়ে দিতে দিতে বলে, আপনি যা ভাবছেন মোটেই তা নয়। ক্লাউস যখন নাৎসিদের লাথি খেয়ে ইংল্যান্ডে পালিয়ে এল তখন প্রথমে আমাদের বাড়িতেই আশ্রয় পায়। ছেঁড়া পালুন, জুতোয় তাপ্লিমারা-নেহাৎ দয়াপরবশ হয়ে আমি তখন আমার পকেট-মানি থেকে
হঠাৎ নিজেই কী ভেবে থেমে পড়ে।
ফুকস্ বলে, কেন মিছে কথা বলছ রোনাটা? সত্যি কথাটা চেপে যাবার চেষ্টা করে লাভ নেই। কর্নেল প্যাশ জাত-গোয়েন্দা। ঠিকই আন্দাজ করছে সে।
-কী সত্যি কথা?–গর্জে ওঠে রোনাটা।
–সে সময় তুমি আমার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলে!
রোনাটা হয়তো মেরেই বসত ফুকসকে। বাধা দিল প্যাশ। বললে, মিসেস কার্ল, আপনি কি ফাইনম্যানের সেই বিখ্যাত তানকাটা শুনেছেন, ডক্টর ফুকসের ওপর।
–’তানকা’ কাকে বলে?
–জাপানি কবিতা–তিন-চার লাইনের। প্রফেসর ফাইনম্যান মুখে মুখে অমন কবিতা-রচনায় সিদ্ধহস্ত। উনি ডক্টর ফুকস্ সম্বন্ধে বলেছেন :
“Fuchs…Looks…An ascetic… Theoretic.” অর্থাৎ ফুকসকে দেখলে মনে হয় ভালো মানুষ। আসলে ডক্টর ফুকস্..পাদপূরণ করে রোনাটা নিজেই–পাজির পা-ঝাড়া! অকৃতজ্ঞ! শয়তান!
ফুকস উঠে দাঁড়ায়। আভূমি নত হয়ে ‘বাও’ করে : থ্যাংকস ফর দ্য কমপ্লিমেন্টস্।
কাজের কথায় আসে প্যাশ। বলে, মিসেস কার্ল, আপনার দ্বারস্থ হয়েছি একটা বিশেষ কৌতূহল মেটাতে। এই ফটোখানি প্রফেসর কার্ল উপহার দিয়েছিলেন ডক্টর ফুককে। এটা তিনি কেমন করে তুলেছেন জানেন?
ফটোখানি হাতে নিয়ে রোনাটা হাসে। বলে, আপনিই বলুন না?
আমি প্রথমে ভেবেছিলাম–ট্রিক ফটোগ্রাফি। দুটো নেগেটিভ সুপার-ইম্পোজ করা। কিন্তু পরে পরীক্ষা করে দেখলাম, তা নয়। আপনি কিছু জানেন?
-জানি। আপনি যে অনবদ্য তানকাটা এই মাত্র শুনিয়েছেন, তার প্রতিদান হিসাবে এ গোপন রহস্যটা আপনার কাছে ফাঁস করে দেব। কেবল একটি শর্তে–প্রফেসরকে বলবেন না। এই ফটোখানা দেখিয়ে সে অনেককে তাক লাগিয়ে দিয়েছে।
বেশ বলব না, এবার বলুন।
এ ছবি একবার মাত্র এক্সপোজ করে তোলা হয়েছে। কোনো ফটোগ্রাফিক ট্রিক এর মধ্যে নেই। এ-পাশে অটো কার্ল, ও-পাশে হান্স কার্ল।
–হ্যান্স কার্ল! তিনি কে?
প্রফেসর কার্ল-এর যমজ ভাই। মস্কোতে আছেন। তিনিও ফিজিসিস্ট।
অনেক কষ্টে কর্নেল প্যাশ তার অভিব্যক্তি গোপন রাখল। কী আশ্চর্য! কী অপরিসীম আশ্চর্য! প্রফেসর অটো কার্লের এক যমজ ভাই আছে, যে নিজেও পদার্থবিজ্ঞানী, সেও নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট এবং মস্কোতে থাকে।
সেদিনই প্রফেসর অটো কার্ল-এর ব্যক্তিগত ফাইলটা প্যাশ আবার হাতড়ে দেখল। হ্যাঁ, ‘কোশ্চেনেয়ারে’ প্রফেসর কার্ল লিখেছেন, তার একটি ভাই আছে। সে বিজ্ঞানী। মস্কোর লেবেডফ ইন্সটিটুটে গবেষণা করছে। তার বয়স যা উল্লেখ করা হয়েছে তা প্রফেসর অটো কার্ল-এর সঙ্গে হুবহু এক। অর্থাৎ একটু অঙ্ক কষলেই এফ. বি. আই. বুঝতে পারত–ওই হান্স কার্ল হচ্ছেন অটো কার্লের যমজ ভাই। এতদিন সে অঙ্কটা কেউ কষে দেখেনি। কিন্তু সেকথা স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করা নেই।
…কাহিনিটা শেষ করে প্যাশ কর্নেল ল্যান্সডেলকে বললে, এবার বলুন স্যার, আপনার একমাসের মাইনে বাজি ধরবেন?
কর্নেল ল্যান্সডেল শুধু বললেন, স্ট্রেনজ!
–অর্থাৎ ওই হান্স কার্ল যদি কোনো ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্ট নিয়ে আমেরিকায় এসে থাকে, এবং প্রফেসর অটো কার্ল-এর আইডেন্টিটি ডিস্ক-এর একটা নকল তাকে রাশিয়ান গুপ্তচরেরা দিয়ে থাকে তাহলে অনায়াসে লস অ্যালামসের প্রতিটি কেন্দ্রে হয়তো সে প্রবেশ করেছে। অপর পক্ষে ছয়ই অগাস্ট ওয়াশিংটনে গ্রোভসের ঘরে যে লোকটা অল্পসময়ের জন্য হাজিরা দেয় সে যদি হান্স কার্ল হয়, তাহলে প্রফেসার অটো কার্ল অ্যালেবাই সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে সান্তা ফে-তে গিয়ে মাইক্রোফিটা হস্তান্তরিত করতে পারেন।
–আই সি।বললেন সংক্ষেপে কর্নেল ল্যান্সডেল।
.
০২.
‘অ্যালেক’ ধরা পড়ল 1946-এর তেসরা মার্চ।
তার মাসতিনেক পরে স্যার জন, প্রফেসর কার্ল আর ডক্টর ফুকস চলে গেলেন হারওয়েলে।
অ্যালেকের প্রকৃত নাম ডক্টর এ্যালেন নান মে। ইংরেজ। যুদ্ধের প্রথম দিকে এসেছিল কানাডায়। সেখান থেকে শিকাগোতে। সে যে খবর পাঠিয়েছিল তা সামান্যই। প্রথমত বোমাটা ইউ-235 এর; দ্বিতীয়ত সে সময় ম্যাগনেটিক সেপারেশনে দৈনিক চারশ গ্রাম ইউ-235 পাওয়া যাচ্ছিল। এ ছাড়া 162 মাইক্রোগ্রাম পরিমাণ ইউ-235 সে ল্যাবরেটরি থেকে পাচার করে এবং রাশিয়ান গুপ্তচরের হাতে সমর্পণ করে। এই তার অপরাধ।
লন্ডনের ওল্ড বেইলি কোর্টে তার বিচার হয়। সংক্ষিপ্ত বিচার। নান দোষ স্বীকার করে। দশবছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে যায় তার।
অ্যালেন নান-এর জবানবন্দী থেকে ডেক্সটার অথবা ডগলাস সম্বন্ধে কোনো তথ্যই জানা গেল না। বস্তুত সে ওই দুজনের সঙ্গে কোনো সময়েই যোগাযোগ করেনি।
ইতিমধ্যে অন্যান্য সূত্র থেকে এটুকু বোঝা গেছে, ডগলাস মধ্য-য়ুরোপের লোক। আমেরিকান বা ইংরেজ নয়। প্যাশ-এর ধারণা ডগলাস এবং ডেক্সটার একযোগে কাজ করেছে। তারা পরস্পরকে চেনে। এ-ক্ষেত্রে তারা নিশ্চয়ই সেই যোগসূত্রটুকু বজায় রেখে চলেছে। এখন দুজনেই দুজনের মৃত্যুবাণ। একজন ধরা পড়লেই অপরজন বেশি করে বিপদগ্রস্ত হবে। এই যুক্তি অনুসারে কর্নেল প্যাশ তীক্ষ্ণ নজর রাখবার ব্যবস্থা করল সম্ভাব্য ডেক্সটারদের ওপর–অর্থাৎ ফাইনম্যান, অটো কার্ল এবং ওপেনহাইমারের সঙ্গে কে কে দেখা করতে আসছে। হারওয়েল থেকে এই সূত্রে তাকে স্কার্ডন জানালো একজনের নাম–ব্রুনো পন্টিকার্ভো। সংক্ষেপে ব্রুনো অথবা পন্টি। জাতে ইটালিয়ান। এনরিকো ফের্মির ছাত্র, কিছুদিন জোলিও-কুরির বিজ্ঞানাগারেও রেডিও অ্যাকটিভিটির ওপর কাজ করেছে। পরে পালিয়ে আসে কানাডায়। ‘চক-রিভার’-প্রকল্পে যুক্ত ছিল। পরমাণু-বোমার বিষয়ে অনেক কিছু জেনেছে সে। যুদ্ধান্তে ফিরে গেছে ইংল্যান্ডে। হারওয়েলে চাকরির ধান্দায় আছে। তাকে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে অটো কার্লের বাড়িতে। মনে হয়, দুজনের দীর্ঘদিনের জানাশোনা। প্রফেসর অটো কার্ল বর্তমানে হারওয়েল ইনস্টিটুটের দু-নম্বর কর্ণধার। প্রধান কর্মকর্তা হচ্ছেন ডিরেক্টর স্যার জন ককট। ব্রিটিশ ডেলিগেশানের কর্ণধাররূপে মানহাটান প্রকল্পে যুক্ত ছিলেন যুদ্ধের সময়। তার অধীনে আছেন প্রফেসর কার্ল। তিন নম্বর চেয়ারে বসেছেন ডক্টর ক্লাউস ফুকস্। শোনা গেল, প্রফেসর কার্ল নাকি ভিতরে ভিতরে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন যাতে ব্রুনো একটা চাকরি পেয়ে যায় ওখানে। কেন?
হারওয়েল-এ প্রথম আবির্ভাবের দিনটির কথা কোনোদিন ভুলবে না রোনাটা। জুন 1946। রৌদ্রকরোজ্জ্বল সুন্দর একটি প্রভাত। অক্সফোর্ড থেকে একটি ট্যাক্সি নিয়ে প্রথম এল ওরা। ওরা তিনজন। প্রফেসর অটো কার্ল, তার স্ত্রী রোনাটা আর ক্লাউস ফুকস্। তার মাসতিনেক আগে আমেরিকা থেকে ফিরে এসেছেন স্যার জন–হারওয়েলের ডিরেক্টার। মালপত্র তখনও এসে পৌঁছায়নি। লন্ডন থেকে ট্রেনে চেপে এসেছিল অক্সফোর্ড। সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে হারওয়েল।
রোদ ঝলমল সবুজ-প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে কুমারী মেয়ের সিঁথির মতো পড়ে আছে সড়কটা। মাঝে মাঝে খামারবাড়ি-যব আর বার্লির ক্ষেত। পাতা-ঝরার দিন শুরু হয়নি, রৌদ্রে ঝলমল করছে সবুজ সতেজ পপলার আর এম গাছের সারি। বিসর্পিল পথে গাড়ি চলেছে। কেউ কোনো কথা বলছে না। নীরবে উপভোগ করছে এই প্রথম আবির্ভাব মুহূর্তটি; আর নতুন যুগে, নতুন পৃথিবীতে নতুন করে বাঁচার প্রভাতী সুর।
হঠাৎ দূর থেকে দেখা গেল পুরানো হারওয়েল গ্রাম। খড়, টালি আর স্লেটের ছাদ। যেন সারি সারি খেলাঘর। চিমনি দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। গ্রাম্য কুকুরগুলো এখনও বোধ হয় মোটর-কারে অভ্যস্ত হয়নি। তারস্বরে প্রতিবাদ জানাচ্ছে তারা। হঠাৎ রোনাটার নজরে পড়ল একটা উঁচু টিলা। তার মাথায় একটা ছোটো বাংলোর মতো মনে হচ্ছে।
-ওটা কী?–কৌতূহলী রোনাটা প্রশ্ন করে।
নিউক্লিয়ার-ফিজিক্স-এর দুই পণ্ডিত শ্রাগ করলেন। অজ্ঞতা প্রকাশ করা ছাড়া উপায় কী? জবাব দিল ক্যাব-ড্রাইভার। বললে, ম্যাডাম, ওটা হচ্ছে ‘হোয়াইট-হর্স অফ উফিংটন। এখানেই একদিন সেন্ট জর্জ সেই ড্রাগনটাকে বধ করেছিলেন। আজ সেই সেন্ট জর্জও নেই, ড্রাগনও নেই–পড়ে আছে শুধু সাদা ঘোড়াটা।
–সাদা ঘোড়াটা! বল কী! এতদিন ধরে আছে?
–আছে ম্যাডাম। বিশ্বাস না করেন তো দেখে আসুন। আমি না হয় আধঘন্টা অপেক্ষা করছি। কারবুরেটারটাও গণ্ডগোল করছে। এই ফাঁকে দেখে নিই।
রোনাটা তো তৎক্ষণাৎ একপায়ে খাড়া। নিষ্ঠাবতী খ্রিস্টান সে। বাইবেল তার কণ্ঠস্থ। সেন্ট জর্জ এখানেই সেই ড্রাগনটাকে বধ করেছিলেন শুনে রোমাঞ্চ হয়েছে তার। গাড়ি থামতেই সে নেমে পড়ে। বলে, এস তোমরা।
বৃদ্ধ প্রফেসর কার্ল বলেন, ওহ মাই! আমাকে মাপ কর ডার্লিং। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত।
তবে তুমিই এস–রোনাটা ডাক দেয় ক্লাউসকে।
ক্লাউস ইতস্তত করে। প্রফেসর কালই তাকে উৎসাহ জোগান-যাও, দেখে এস। আমি বরং এখানেই আছি। একটু পায়চারি করি ততক্ষণে।
পায়ে পায়ে ওরা দুজন এগিয়ে চলে। রোনাটা আর ক্লাউস। বিসর্পিল পথে পাকদণ্ডীর একটা মোড় ঘুরেই রোনাটা বলে, তুমি অত মুখ গোমড়া করে আছ কেন বলতো ক্লাউস? জোর করে ধরে আনলাম বলে?
জোর করে মানে? আমি তো স্বেচ্ছায় এ চাকরি নিয়েছি। তোমার উপরোধ পড়ে মোটেই নয়।
-জানি। আমার উপরোধে পড়ে তুমি কবে কোন্ কাজটা করেছ?
মনে মনে কাঁটা হয়ে ওঠে ক্লাউস। এই প্রসঙ্গটিকে সে সবচেয়ে ডরায়। সে কিছুতেই ভুলতে পারে না সাত-আট বছর আগেকার একটা ঘটনা–চিরাচরিত রীতি লঙ্ঘন করে কুমারী রোনাটাই একদিন প্রস্তাব তুলেছিলক্লাউস ফুকসকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তার জীবনের ভোগে। ক্লাউস নিজেই সে প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করেছিল সেদিন। তাই প্রসঙ্গটা ঘোরাবার জন্য তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, সেন্ট জর্জ আর ড্রাগনের ব্যপারটা কী?
পথের মাঝখানেই থমকে পড়ে রোনাটা। প্রতিপ্রশ্ন করে, তুমি কি খ্রিস্টান?
–আমার বাবা তো বটেই!
–বাবার কথা তুলো না! তার নাম উচ্চারণ করারও যোগ্য নও তুমি।
–কী মুশকিল। আমার বাবার নাম আমি বলব না?
–না বলবে না। যে সেন্ট জর্জের নাম শোনেনি—
টিলার মাথায় সত্যই ছিল একটা অদ্ভুত জিনিস। প্রায় দু-হাজার বছরের প্রাচীন ছবি। পাথরের গায়ে খোদাই করে আঁকা-ঘোড়া একটা। সাদা চকের পাহাড়, তাই ওটা সাদা ঘোড়া। কিংবদন্তির সেন্ট জর্জ নাকি সাদা ঘোড়ায় চড়ে গিয়েছিলেন ড্রাগনকে বধ করে বন্দিনী ‘ড্যামসেল-ইন-ডিস্ট্রেস’কে উদ্ধার করে আনতে। বিগত যুগের ওই শিল্পকর্মটি দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে যাত্রীরা আসে হারওয়েলে।
টিলার ওপর থেকে দেখা গেল ট্যাক্সিটা। খেলাঘরের গাড়ি যেন। প্রফেসর কার্ল পায়চারি করছেন; আর বনেট খুলে ক্যাব-ড্রাইভার হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ইঞ্জিনের ওপর।
পাকদণ্ডী পথে ফেরার সময় রোনাটা বললে, আচ্ছা ক্লাউস, ধর আমি যদি একদিন ওইরকম বন্দিনী হয়ে পড়ি–তুমি অমন সাদা ঘোড়ায় চেপে আমাকে উদ্ধার করতে আসবে।
হঠাৎ আকাশ-ফাটানো অট্টহাস্য করে ওঠে ক্লাউস। বলে, কী পাগল তুমি, রোনাটা! এযুগে কি ড্রাগন পাওয়া যায় পথে-ঘাটে?
রোনাটা অপ্রস্তুত হল না মোটেই। বললে, কেন পাওয়া যাবে না? হয়তো তার চেহারাটা পালটেছে–তাই সহজে চেনা যায় না; কিন্তু ড্রাগন আছে বইকি আজও।
ওর কথার মধ্যে কী যেন একটা বেদনার সুর ছিল। চমকে উঠল ক্লাউস।
***
হারওয়েল জায়গাটাকে কিন্তু ভালো লেগে গেল ক্লাউস ফুকস-এর। শুধু জায়গাটাই নয়, গোটা প্রকল্পটা। আলাদিনের আশ্চর্য-প্রদীপ থেকে ওঁরা বার করেছেন একটা দৈত্যকে–কিন্তু তাকে দেওয়া হল শুধুমাত্র ধ্বংসের আদেশ। এ ঠিক হয়নি–এজন্য এ গুপ্তধনের সন্ধানে প্রাণপাত করেননি-রাদারফোর্ড-কুরি দম্পতি-চ্যাডউইক-ফের্মি আর অটো হান। হ্যাঁ, ফুকস্ স্বীকার করে, প্রথম সাফল্যে সে নিজেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে মদ কিনতে ছুটেছিল–কিন্তু সেটাই শেষ কথা নয়। এতদিনে সে পথের সন্ধান পেয়েছে। মানব-কল্যাণে যদি এই মহাশক্তিকে কাজে লাগানো যায়, তবেই সার্থক হবে অর্ধশতাব্দীব্যাপী বিজ্ঞানীদের সাধনা। সেই আয়োজনই হচ্ছে হারওয়েলে। মনপ্রাণ তাই ঢেলে দিল ফুকস্।
সমস্ত কারখানাটা উঁচু কাটা-তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা। সামনে লোহার বড় গেট। বন্দুকধারী পাহারা। তাকে ‘পাস্ দেখিয়ে তবে তুমি ঢুকতে পারবে এ-রাজ্যে। ঢুকতেই সামনে একটি দ্বিতলবাড়ি। অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস। এখানেই কাজ করতে হয় তাকে। স্যার জনের পাশের ঘরে। ও-পাশে প্রফেসর কার্লের অফিস। আগে এটা ছিল রয়েল এয়ার ফোর্সের একটা আস্তানা। বিমানবাহিনীর কর্মীদের ঘরগুলোই পাওয়া গিয়েছে আপাতত। নতুন নতুন বাড়িও হচ্ছে। একতলা বাড়ি সব–সামনে ফুলের বাগান, পিছনে সবজির। স্টাফ-কোয়ার্টার্সকে বাঁ-হাতে রেখে যদি এগিয়ে যাও তাহলে আবার একটা কাঁটাতারের বেড়ার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে। আবার পাস দেখাতে হবে। ভেতরটা কারখানা নয়, বিজ্ঞানগার। সবচেয়ে অবাক হয়ে যাবে অ্যাটমিক পাইলটাকে দেখে। প্রকাণ্ড একটা গোলাকৃতি গম্বুজ–যেন রোমের কলোসিয়ামের অনুকৃতি। ওর কাছে গিয়ে দাঁড়াতে ভয় হবে তোমার। সজ্ঞানে হয়তো ঠিক হিরোশিমা-নাগাসাকির কথা মনে পড়বে না, তবুও গা-ছমছম করবে। মনে হবে অজানা-অচেনা এক অরণ্যের মাঝখানে এসে পড়েছ বুঝি। চারদিক ঝকঝক তকতক করছে–হ্যাঁসপাতালের অপারেশন থিয়েটার যেন। হঠাৎ নজরে পড়বে একটা বিজ্ঞপ্তি : ধূমপান নিষেধ। হয়তো ধড়াস করে উঠবে বুকের ভেতর। হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা কোথায় ফেলবে ভেবে পাবে না। তখনই একজন কর্মী হয়তো এগিয়ে আসবে, বলবে–অমন আঁৎকে উঠবেন না স্যার; অ্যাটমিক-পাইলটা কোনো ডিনামাইটের স্তূপ নয়–সিগারেটের আগুনে ওটা জ্বলে। উঠবে না। ওই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া আছে যাতে জায়গাটা নোংরা না হয়।
ফুকস্ আর কার্ল এখানে পৌঁছানোর বছর দেড়েক আগেই এ প্রকল্পে হাত দেওয়া হয়েছে। এখন এখানে শ-দুয়েক কর্মী কাজ করে। তার মধ্যে জনাত্রিশেক হচ্ছে বিজ্ঞানী। বিজ্ঞান-চর্চা তারা করেছে সামান্যই, জ্ঞানও অল্প। বয়স বিশ-পঁচিশ। আসলে ওরা সবাই যুদ্ধ-ফেরত। ফিজিক্সের চর্চা ছেড়েছে তিন-চার বছর আগে–কেমব্রিজ-অক্সফোর্ড- হ্যাঁরো-ইটনে। চলে গিয়েছিল মরণপণ যুদ্ধে–ওরা মূলত টেকনিশিয়ান, হাতে-কলমে কলকজার কাজই শুধু জানে। স্যার জন তাই ব্যবস্থা করেছেন সপ্তাহে চারদিন তাদের নিয়ে থিওরেটিক্যাল ক্লাস করতে হবে। ক্লাস নেন তিনি নিজে, আর তার দুই সহকর্মী–প্রফেসর কার্ল আর ডক্টর। ছেলেগুলো প্রাণবন্ত-মৃত্যুকে বারে বারে দেখেছে চোখের সামনে। নীতিবাধের বালাই কম-কিন্তু নতুন পৃথিবী গড়ে তোলার সংকল্প আছে।
ওঁরা তিনজনই মাত্র পদস্থ অফিসার-বাদবাকি তো ছেলে-ছোকরা। আরও দুজনের সঙ্গে আলাপ হয়েছে ফুকস-এর। উইং-কমান্ডার হেনরি আর্নল্ড আর ডক্টর স্যামুয়েল স্কট। আর্নল্ড ছিলেন বিমানবাহিনীতে, প্রৌঢ় গম্ভীর স্বভাবের মানুষ, বিপত্নীক। তিনি হারওয়েলের স্পেশাল সিকিউরিটি অফিসার। এখানে অবশ্য সিকিউরিটির অতটা কড়াকড়ি নেই, যেমন ছিল লস অ্যালামসে। সেখানে প্রত্যেকের ছদ্মনাম ছিল, স্বনামে কারও পরিচয়ই ছিল না। এখানে সেসব কিছু নেই। তবু পারমাণবিক-তত্ত্বের পরীক্ষা-নিরীক্ষা যখন হচ্ছে তখন গোপনীয়তার প্রয়োজন আছে বইকি। আর ডক্টর স্কট এখানকার মেডিক্যাল অফিসার। ছোটো একটা আউটডোর ডিসপেন্সারি আছে তার। অমায়িক মানুষ। আছেন সপরিবারে, স্ত্রীপুত্র পরিজনদের নিয়ে। সুখী পরিবার।
এখানে এসে এতদিন পরে ক্লাউস-এর মনে হচ্ছে, জীবনে নোঙর ফেলার দিন এসেছে বুঝিবা। এখন ওর বয়স পঁয়ত্রিশ। এতদিন সংসার করার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। এখন আর পাঁচজনের পরিবারের দিকে তাকিয়ে ওরও মনে হচ্ছে এই নির্বান্ধব ব্যাচিলারের জীবনে সে কোনদিনই শান্তি পাবে না। 1946-এ প্রথম যখন। চাকরিতে ঢোকে তখন ওর রোজগার ছিল বছরে 275 পাউন্ড, এখন উপার্জন করছে 1,500 পাউন্ড। অর্থাৎ মাসে প্রায় আড়াই হাজার টাকা। 1946-এ যুদ্ধোত্তর ইংল্যান্ডে এ উপার্জন বড় কম নয়। কিন্তু বিবাহ করে সংসার করায় তার একটি প্রচণ্ড বাধাও আছে। সে বাধা–ফ্রাউ রোনাটা কার্ল।
***
এ ধাঁধার সমাধানটা বুঝতে হলে ক্লাউস ফুকস্-এর অতীত জীবনটাকে জানতে হবে। ক্লাউস জার্মানি থেকে প্রাণ নিয়ে যখন ইংল্যান্ডে পালিয়ে এসেছিল তখন ওর বয়স মাত্র বাইশ। জার্মানির কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন উৎসাহী ছাত্রনেতা ছিল সে। রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে সে ছিল ন্যাশনাল সোসালিস্ট পার্টির বিরুদ্ধ দলে। ছাত্র-আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। হঠাৎ দেখা গেল ওর বিরুদ্ধ দল, ওই ন্যাশনাল সোসালিস্ট পার্টি, জার্মানির ক্ষমতা দখল করেছে তার নাম হয়েছে নাৎসি পার্টি। ওই দলের নেতা অ্যাডলফ হিটলার হয়েছে জার্মানির দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। 1933-এর তিরিশে জানুয়ারি–যেদিন হিটলার জার্মানির ক্ষমতা দখল করল, সেদিন কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে হিটলারের অনুগামীরা তন্নতন্ন করে খুঁজেছিল বিপক্ষদলের ওই ছাত্রনেতাকে–পাদরি ফুকসের সেই দুর্বিনীত পুত্র ক্লাউস-কে। খবর পেয়ে ক্লাউস আত্মগোপন করে। প্রথমে পালিয়ে যায় পারিতে, সেখান থেকে কপর্দকহীন অবস্থায় ইংল্যান্ডে।
ফ্রলাইন রোনাটা হেল্মহোল্টৎজ-এর বয়স তখন মাত্র সতেরো। হাইস্কুলের ছাত্রী। তার বাবা ছিলেন পাদরি ফুকসের একজন গুণগ্রাহী। ফুকস্ আশ্রয় পেল তার পরিবারে। সমারসেট-এ। মিস্টার হেল্মহোল্টজ বিপত্নীক। তার বড় মেয়ে ফ্রলাইন রোনাটাই ছিল গৃহকর্ত্রী–মাত্র সতেরো বছর বয়সে। আরও দুটি ছোটো ছোটো ভাইবোন-এর দায়িত্ব ছিল তার ওপর। এর ওপর এসে জুটল। ক্লাউস-বাইশ বছরের প্রাণবন্ত তরুণ ফুকস ভর্তি হল ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ে। চার। বছর সে ছিল এই পরিবারে, রোনাটার অভিভাবকত্বে। শুধু তাই নয়, রোনাটা ছিল তার মাস্টারনি, দিদিমণি আর কি। তার কাছেই ইংরেজি ভাষাটা শিখেছিল। পরিবর্তে ক্লাউস রোনাটার শক্ত শক্ত অঙ্কগুলো কষে দিত। সে সময় ক্লাউস ছিল মুখচোরা, বইপোকা। চার বছর পরে ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে যে বছর দর্শন ও অঙ্কশাস্ত্রে ডক্টরেট পায় রোনাটা সে বছরই গ্রাজুয়েট হল। আর সেই বছরই মারা গেলেন ওর আশ্রয়দাতা–রোনাটার বাবা।
জার্মান বিজ্ঞানের সেই দুর্লভ প্রতিভা বাস্তুচ্যুত মাক্স বর্ন তখন এডিনবরায় পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। ক্লাউস ফুকস-এর প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন এবং তার অধীনে একটি স্কলারশিপ জুটিয়ে দেন। ক্লাউস সমারসেট ছেড়ে চলে আসে স্কটল্যান্ডে, এডিনবরায়।
সেই বিদায়মুহূর্তেই ঘটল একটা ঘটনা যার প্রতিক্রিয়া সারাজীবন ধরে অনুভব করছে ক্লাউস। রোনাটা ততদিনে একটা চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে। সংসারটা চালাবার মতো ব্যবস্থা হয়েছে তার। একুশ বছরের তারুণ্যে ভরপুর। ক্লাউস এতদিনে প্রফেসর ম্যাক্স বর্নের অধীনে রিসার্চ করার সুযোগ পেয়েছে শুনে সে অভিনন্দন জানাতে এল ক্লাউসকে। কথা প্রসঙ্গে বললে, তুমি তো এবার এডিনবরায় চলে যাচ্ছ। আমাদের সঙ্গে এই বোধহয় ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।
ক্লাউস বললে, তা কেন? এডিনবরা এমন কিছু সাগরপারে নয়। যোগাযোগ রাখলেই রাখা যেতে পারে। অবশ্য তোমার যদি গরজ থাকে।
–আমার? কী মনে হয় তোমার?
–কী জানি। চিঠি লিখলে জবাব দেবে তো?
হঠাৎ মুখটা নিচু করলে রোনাটা। বললে, আর আমি যদি বলি–চিঠি লেখার দূরত্বে থাকতে চাই না আমি?
-মানে?
ওর চোখে চোখ রেখে রোনাটা বললে, আমি তোমার কাছেই থাকতে চাই। লেটস্ গেট ম্যারেড, ক্লাউস।
–তা কেমন করে সম্ভব? আমার ছাত্রজীবন এখনও শেষ হয়নি।
একটা দীর্ঘশ্বাস পড়েছিল রোনাটার। তারপর বললে, আমি কি তাহলে তোমার প্রতীক্ষায় থাকব?
এবার জবাব দিতে দেরি হল ফুকস-এর। একটু ভেবে নিয়ে বললে, আমি দুঃখিত রোনাটা। তা হবার নয়। বাধা যে কী, তা তোমাকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। কিন্তু আমি আমার জীবনের সঙ্গে তোমাকে কোনোদিনই জড়িয়ে নিতে পারব না।
স্তম্ভিত হয়ে গেল যেন রোনাটা। বহু কষ্টে সে আত্মসম্বরণ করল। তারপর প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে বললে, তাহলে তোমার আগের প্রশ্নটার জবাব দিই, আমাকে চিঠি লিখ না। কারণ জবাব আমি দেব না।
ক্লাউস শুধু বলেছিল, আয়াম সরি।
ঝড়ের বেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল রোনাটা।
***
সে আজ নয়-দশ বছর আগেকার কথা। ক্লাউস কিন্তু ওর কথা মেনে নেয়নি। এডিনবরায় পৌঁছে চিঠি লিখেছিল। একাধিক পত্র। রোনাটাও ছিল তার সংকল্পে অটুট। একটি চিঠিরও জবাব দেয়নি। তারপর যেমন হয়। ক্রমশ ক্লাউস ভুলে গেল তার প্রথম যৌবনের বান্ধবীকে। তিন বছর পর ম্যাক্স বর্নের কাছে থিসিস দাখিল করে পেল ডক্টর অফ সায়েন্স উপাধি। ইতিপূর্বে হয়েছিল পিএইচ. ডি.এবার হল ডি. এসসি.। খবরটা উৎসাহভরে জানালো রোনাটাকে।
এবারও কোনো জবাব এল না।
ক্লাউস ক্রমশ ভুলে গেল মেয়েটিকে। তারপর রোনাটার সঙ্গে ওর দেখা হল সুদূর সাগরপারের দেশে। আমেরিকায়। লস অ্যালামসে। ততদিনে রোনাটা হয়েছে মিসেস কার্ল। একটি সন্তানের জননী। দুর্ভাগ্যক্রমে সন্তানটি বাঁচেনি। তাকে চোখেই দেখেনি ক্লাউস। দেখেছে ফটো। অসংখ্য ফটো। একটা গোটা অ্যালবাম ভরা ছিল অ্যালিসের ছবিতে। রঙিন ছবি। সদ্যোজাত অবস্থা থেকে তার সংক্ষিপ্ত তিন-বছরের জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত। প্রফেসর কার্ল-এর ছিল ফটো তোলার বাতিক। রঙিন ছবিও তুলেছেন অনেক। মুভি ক্যামেরাতেও। তাই চোখে না। দেখলেও রোনাটার কন্যা অ্যালিসকে ক্লাউস ভালোভাবেই চেনে। মেয়েটা রোনাটার মতো দেখতে হয়নি মোটেই। রোনাটা ‘ব্লন্ডি’–সোনার বরণ তার। মাথাভরা চুল, রোনাটার মুখটা টিকলো–মেয়েটি ছিল ‘ব্রুনেট’; তার মুখটাও গোলগাল।
রোনাটার চেয়ে তার স্বামী বাইশ বছরের বড়। এমন বিবাহে রোনাটা যে জীবনে সুখী হয়নি তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এমন অসম বয়সের পুরুষকে কেন পছন্দ করল রোনাটা? এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পায়নি ক্লাউস। জিজ্ঞাসাও করা যায় না এ কথা। প্রফেসর কার্ল মহাজ্ঞানী-অধ্যাপক অথবা পণ্ডিত হিসাবে তাকে যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয় নির্বাচন করবে; কিন্তু পঁচিশ বছরের একটি মেয়ে তার কোন্ গুণে অভিভূত হয়ে স্বামী হিসাবে তাকে নির্বাচন করল?
তাই আজ এতদিন পরে সেই মেয়েটির চোখের সামনেই সংসারী হতে কেমন যেন অস্বোয়াস্তি বোধ করে ক্লাউস। বান্ধবী তার হয়েছে অনেক। তার রূপ, যৌবন এবং রোজগার দেখে অনেক মেয়েই উৎসাহ বোধ করছে। ও নিজেই কেমন যেন অপরাধী বোধ করে তাতে। মদের মাত্রাটা বাড়িয়ে দেয় শুধু।
হারওয়েলে এসে আরও একটা অনুভূতি হয়েছে। তার মনে হয়, সর্বদাই যেন একজোড়া অদৃশ্য চোখ লক্ষ্য করছে ওকে–ওকে নয়, ওদের। প্রফেসর কার্ল, রোনাটা আর ক্লাউসকে ক্রমাগত লক্ষ্য করে যাচ্ছে কেউ। প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই, কিন্তু সর্বদাই যেন এক অদৃশ্য সন্ধানীর দৃষ্টির শিকার হয়ে রয়েছে ওরা। কেন এমন মনে হয় ওর? রোনাটার প্রতি তার, অথবা তার প্রতি রোনাটার অন্তরে যে গোপন অনুভূতি আছে সেটাই কি আবিষ্কার করতে চায় ওই অদৃশ্য গোয়েন্দা চোখজোড়া? স্যোসাল স্ক্যান্ডাল? বুঝে উঠতে পারে না। শেষ পর্যন্ত একদিন সে মরিয়া হয়ে এসে হাজির হল হেনরি আর্নল্ডের দরবারে। খুলে বললে তার ওই অদ্ভুত অনুভূতির কথা। সব কথা শুনে হো-হো করে হেসে উঠল আর্নল্ড। বললে,–না না, ডক্টর ফুকস, আমি আপনার পেছনে কোনো গোয়েন্দা লাগাইনি। বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যা। সুন্দরী মিসেস কার্ল এবং যৌবনদীপ্ত প্রফেসর ফুকস্ যে পরস্পরকে কী চোখে দেখেন, তা আমার ভালোই জানা আছে। এবং এ কথাও জানি যে, মিসেস রোনাটা কার্লের প্রাকবিবাহ জীবনের বন্ধু ছিলেন আপনি। নিশ্চিত থাকুন ডক্টর ফুকস, আপনাকে কোনো সামাজিক কেলেঙ্কারির মধ্যে ফেলবার শুভ উদ্দেশ্য আমার আদৌ নেই।
ডক্টর ফুকস্ রাঙিয়ে ওঠে। বলে, না না, আপনার বিরুদ্ধে আমা? কোনো অভিযোগ নেই। আপনি গোয়েন্দা লাগিয়েছেন এ কথাও বলছি না। কি আমার এমন মনে হচ্ছে কেন?
এর জবাবে হেনরি আর্নল্ড হ্যামলেট থেকে একটি উদ্ধৃতি শুনিছিলেন— ডক্টর অফ ফিলসফি তার দর্শনের মাধ্যমে যে স্বপ্ন দেখতে অক্ষম তাও নাকি দুনিয়ায় সম্ভব।
আদ্যোপান্ত কিছু বোঝা যায় না। উঠে আসছিল ক্লাউস। তাকে আবার ফিরে ডাকল আর্নল্ড, বাই দ্য ওয়ে ডক্টর, এই ফটোগুলো দেখুন তো। এদের কাউকে চেনেন?
খান তিন-চার ফটো বার করে দেখায়। ক্লাউস ছবিগুলো উল্টেপাল্টে দেখে। আর্নল্ড বলে, এঁদের কাউকে কখনও লস অ্যালামসে দেখেছেন? ধরুন প্রসের কার্ল-এর বাড়িতে?
–হ্যাঁ, এঁকে দেখেছি। এঁকে চিনিও। এঁর নাম ডক্টর অ্যালেন নান মে।
–আর দুজনকে?
–না চিনি না। কিন্তু কেন বলুন তো? কে এঁরা?
–আপনি খবরের কাগজ পড়েন না?
–বিশেষ নয়। কেন?
–ডক্টর অ্যালেন নান মে-র নাম এ সপ্তাহে প্রতিদিন খবরের কাগজে ছাপা হচ্ছে। দেখেননি?
–না। কেন? তিনি কি নতুন কিছু আবিষ্কার করেছেন?
-না। বাড়ি গিয়ে ক-দিনের পুরানো খবরের কাগজ উল্টে দেখবেন। আর একটা কথা। এখানে, এই হারওয়েলে-বিশেষ করে প্রফেসর কার্ল-এর বাড়িতে–অস্বাভাবিক কিছু দেখলে আমাকে গোপনে এসে জানিয়ে যাবেন।
অবাক হয়ে যায় ক্লাউস। বলে, কেন বলুন তো? কী ব্যাপার?
আর্নল্ড জবাব দেয় না। র্যাক থেকে খানকতক ‘লন্ডন টাইমস’ নিয়ে গুঁজে দেয়। ওর হাতে। বলে, শুধু নিউক্লিয়ার ফিজিকস্ পড়লেই চলবে না ডক্টর, একটু-আধটু দুনিয়ার খবরও রাখতে হবে। যান, এগুলো পড়ে দেখুন। আপনার প্রশ্নের জবাব ওতেই পাবেন।
তা পেল ক্লাউস। কাগজে সাড়ম্বরে বার হয়েছে অ্যালেন নান মের গুপ্তচরবৃত্তির কাহিনি।
***
তার দিনসাতেক বাদে ঘটল ঘটনাটা। অদ্ভুত একটা অভিজ্ঞতা।
কী একটা কাজে ক্লাউস এক সপ্তাহান্তে লন্ডনে গিয়েছিল। একাই মাসে দু-একবার সে এভাবে শহরে যেত। সঙ্গে নিয়ে যেত লম্বা লিস্ট। হারওয়েল মিসেসদের নানান শৌখিন জিনিসের অর্ডার। কোনো কোনো দিন রবিবারটা সে লন্ডনেই কাটিয়ে আসত–কোনো হোটেলে। সেবার কী মনে হল, ও ফিরে আসবে বলে স্থির করল। সাউথ কেনসিংটন স্টেশনের দিকে যাচ্ছে, হঠাৎ পথের মাঝখানেই ওকে পাকড়াও করলেন প্রফেসর কার্ল, কোথায় চলেছ হে?
-হারওয়েলেই ফিরব। আপনি এখানে?
-ওয়েম্বেলেতে গিয়েছিলাম। জি. ই. সি. কোম্পানিতে। কাজ মিটে গেল, এখন ফিরে যাচ্ছিলাম।
প্রফেসর কার্ল গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। নিজের গাড়ি। এখানে এসে কিনেছেন। নিজেই ড্রাইভ করছেন। ফুকস্ উঠে বসল ওঁর পাশে। মালপত্র তুলে দিল পিছনের সিটে।
–প্যারাম্বুলেটার কী হবে হে? তুমি তো ব্যাচিলার।
–ওটা মিসেস স্কটের অর্ডার। ডাক্তারবাবুর বাচ্চার জন্য।
–বেশ আছ তুমি। এবার নিজের ল্যাজটা কাটো। আমাদের দলে নাম লেখাও।
ক্লাউস হাসল। জবাব দিল না।
শহর ছেড়ে শহরতলীতে এল ওরা। ক্রমে অক্সফোর্ডের দিকে ফাঁকা রাস্তায় পড়ল। বেলা তখন পাঁচটা। গ্রীষ্মকাল। সূর্য অস্ত যেতে তখনও ঘণ্টাচারেক। বেশ রোদ আছে। ফাঁকা অ্যাসফল্টের রাস্তায় পড়ে স্পিড বাড়ালেন প্রফেসর। বললেন, অনেকদিন আমার বাড়ি আসছ না তো। কেন?
কী বলবে ক্লাউস? প্রফেসর কার্ল-এর বাড়ি তাকে টানে; কিন্তু ইচ্ছে করেই সে এড়িয়ে চলে। রোনাটার মুখোমুখি দাঁড়ালেই আজকাল সে বিবেকের দংশন অনুভব করে। রোনাটা দিন দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। বেশ রোগা হয়ে গিয়েছে। মানসিক অবসাদে ভুগছে যেন। দেখলেই মনে হয়, মেয়েটা অসুখী। ওর নীরবতাকে পাত্তা না দিয়ে প্রফেসর আবার বলেন, সময় পেলে এস। মাঝে মাঝে তোমাকে দেখলে রোনাটা তবু একটু খুশি হয়।
কেমন আছে সে আজকাল?-মামুলি প্রশ্ন।
–ভালো নেই ক্লাউস। মাঝে মাঝে ফিট হচ্ছে আজকাল।
–ফিট হচ্ছে! কেন? ডক্টর স্কট দেখেছেন? কী বলছেন তিনি?
–বলছেন মানসিক অসুখ। সাইকিয়াট্রিস্টকে দিয়ে দেখাতে বলছেন।
–আশ্চর্য তো। এ খবর তো জানতাম না।
–এস একদিন, কেমন? কালই এস না। কাল তো রবিবার। আমার ওখানে ডিনার খাবে। ডক্টর ব্রুনোর সঙ্গেও আলাপ হয়ে যাবে।
–ডক্টর ব্রুনো কে?
–কাল এস। আলাপ করিয়ে দেব।
***
সূর্য পশ্চিম দিগ্বলয়ে হেলে পড়েছে। সড়ক জনমানব শূন্য। অক্সফোর্ড রোডে ওরা তখন গেরার্ড ক্রস আর বেকন্সফিল্ডের মাঝামাঝি। সন্ধ্যা তখন ঠিক ছটা বেজে সাত মিনিট। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ কী একটা বস্তু এসে প্রচণ্ড আঘাত করল সামনের উইন্ডস্ক্রিনে। চৌচির হয়ে ফেটে গেল সেটা। গাড়ি তখন ঘণ্টায় ষাট কিলোমিটার বেগে যাচ্ছিল। ক্লাউস ফুকস্ এ আকস্মিক ঘটনায় একেবারে ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে। তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে যেন। প্রফেসর কিন্তু নির্বিকারভাবে মাইলতিনেক অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে এলেন। তারপর গাড়ি থেকে নেমে ভাঙা উইন্ডস্ক্রিনটা পরীক্ষা করে বললেন–ইট মেরেছে কেউ।
ততক্ষণে অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে ক্লাউস। ইতিমধ্যে সে লক্ষ্য করে দেখেছে, ড্রাইভার আর তার সিটের মাঝামাঝি খাড়াপিঠ গদির মাঝখানে একটা নিটোল ছোট্ট গর্ত হয়েছে। তার ভিতর আঙুল চালিয়ে সে উদ্ধার করে আনল ছোট্ট একটা সীসার গোলক। বললে, না। একটা রাইফেল থেকে ছোঁড়া হয়েছে এটা।
প্রফেসর কার্ল গুলিটাকে হাতে নিয়ে পরীক্ষা করলেন অনেকক্ষণ ধরে। তারপর বললেন, ঠিক বলেছ। এটা রাইফেলের গুলি বলেই মনে হচ্ছে। নিশ্চয় কোনো শিকারীর কাণ্ড। খরগোশ মারতে গিয়ে আমাদের শেষ করে ফেলেছিল একেবারে।
পাহাড়ের ওপরে চারিদিকে তাকিয়ে দেখেন। খুঁজতে থাকেন শিকারীকে।
ক্লাউস বললে, বুলেটটা দিন। ওটা আর্নল্ডকে দেখাতে হবে।
-পাগল। ঘুণাক্ষরেও এ-কথা ওকে বোলো না। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। আমাদের ধরে টানাটানি শুরু করবে। নাও ওঠ। চল, ফেরা যাক।
ফুকস গাড়িতে ওঠে না। বলে, প্রফেসর, আপনি একটা কথা খেয়াল করছেন না। এখানে বাঘ, হরিণ বা বাইসন নেই। খরগোশ মারতে শিকারীরা এ অঞ্চলে আসে বটে, কিন্তু খরগোশ শিকারে কেউ এ জাতীয় বুলেট ব্যবহার করে না।
ভ্রূদুটি কুঁচকে যায় প্রফেসর কার্লের। গম্ভীর হয়ে বলেন–কী বলতে চাইছ তুমি?
–আমি বলতে চাইছি, কেউ আপনাকে অথবা আমাকে হত্যা করবার উদ্দেশ্য নিয়ে একটা রাইফেল থেকে এটা ফায়ার করেছে। খবরটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখনই গিয়ে আমাদের আর্নল্ডকে সব কথা বলতে হবে।
দু-এক মিনিট চুপ করে বসে থাকেন প্রফেসর। তারপর গম্ভীরভাবে বলেন, আমার সেটা ইচ্ছে নয়।
–আমি এক শর্তে ব্যাপারটা গোপন রাখতে রাজি আছি।
চমকে মুখ তুলে ওর দিকে তাকালেন প্রফেসর কার্ল-কী শর্তে?
–আপনি যদি স্বীকার করেন, আমাকে নয়–আপনাকে গুলি করতেই হত্যাকারী গুলিটা ছুঁড়েছে।
-বাঃ। তা কেমন করে জানব আমি?
–আপনি জানতেন। না হলে উইন্ডস্ক্রিনটা চুরমার হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি ব্রেক কষতেন। এমন দশ মিনিট পাগলের মতো ড্রাইভ করে এসে তিন মাইল দূরে গাড়ি দাঁড় করিয়ে পাহাড়ের ওপর শিকারীকে খুঁজতেন না।
মুখটা সাদা হয়ে গেলো প্রফেসর কার্লের। জবাব দিতে পারলেন না তিনি।
–দ্বিতীয়ত, ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না-রাইফেল দিয়ে এমন বুলেটে যে খরগোশ শিকার করা হয় না, তা আপনারও জানা ছিল। এবং তৃতীয়ত, আমি ঘটনাচক্রে এ গাড়িতে উঠেছি। হত্যাকারী অনেক আগে থেকেই এখানে আপনার পথ চেয়ে বসে আছে। আমি যে এ-গাড়িতে ফিরব-তা সে আদৌ জানত না। জানতে পারে না।
আবার অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকলেন প্রফেসর কার্ল। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে বললেন, ডক্টর ফুক। প্রত্যেকের জীবনেই এমন কিছু অধ্যায় থাকে যা অন্যকে বলা যায় না। আমি স্বীকার করছি–আমাকে হত্যা করবার জন্যই রাইফেলধারী এ কাজ করেছে। কিন্তু আমি চাই না সেটা উইং কমান্ডার আর্নল্ড জানতে পারুক। সময় হলেই আমি তাকে বলব। কথা দাও, তুমি নিজে থেকে কিছু বলবে না?
-বেশ। জিজ্ঞাসিত না হওয়া পর্যন্ত আমি এ-কথা তাকে জানাব না।
–ধন্যবাদ।
এতদিনে একটা সমস্যার সমাধান হল ক্লাউস ফুকস-এর : কেন ওর মনে হত একজোড়া অদৃশ্য চোখ ওদের দিবারাত্র পাহারা দিয়ে চলেছে। অদৃশ্য চোখের শিকারী সে নয়, রোনাটা নয়–প্রফেসর অটো কার্ল!
***
পরদিন প্রফেসর কার্ল-এর বাসায় গিয়ে আলাপ হল আর একটি পরিবারের সঙ্গে। ডক্টর ব্রুনো পন্টিকার্ভো। প্রফেসর কার্ল-এর বন্ধু-বন্ধু ঠিক নয়, বয়সে অনেক ছোটো। ক্লাউস-এর চেয়েও দু বছরের ছোটো। সে সপরিবারে এসে উঠেছে প্রফেসর কার্ল-এর বাসায় অতিথি হয়ে। নামকরা নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট। প্রফেসর কার্ল অত্যন্ত স্নেহ করেন তাকে। হারওয়েলে তার যাতে একটি চাকরি হয় তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। ক্লাউস থাকে ব্যাচিলার্স ডর্মিটারিতে, কিন্তু প্রফেসর কার্ল পাঁচ-কামরার বাংলো পেয়েছেন। সংসারে তো কুল্লে দুটি প্রাণী–স্বামী-স্ত্রী। তাই বাকি দুখানা ঘর ছেড়ে দিয়েছেন ব্রুনো পরিবারকে।
ব্রুনো ইটালিয়ান। জন্ম পিসায়। বৃহৎ পরিবারের সন্তান। সাত-আটটি ভাইবোন। তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সারা পৃথিবীতে। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। প্রিয়পাত্র ছিল এনরিকো ফের্মির। তার অধীনে গবেষণা করেছে রোমে থাকতে। সেখান থেকেই ডক্টরেট করে। পরে চলে আসে পারিতে। সেখানে জোলিও কুরির গবেষণাগারে রিসার্চ করে। এখানেই সে বিবাহ করে–হেলেনকে। তার কুমারী জীবনের নাম হেলেন মেরিয়ান। সুইডেনে বাড়ি। স্টকহমে ছিল তার বাপ-মা। ওদের তিনটি সন্তান–জিল, টিটো আর অ্যান্টোনিও। অ্যান্টোনিও সবার ছোটো। বছরদেড়েকের ফুটফুটে বাচ্চা। তিনটি বাচ্চাকে পেয়ে রোনাটার বঞ্চিত মাতৃত্ব যেন এতদিনে একটা অবলম্বন খুঁজে পেয়েছে। হেলেনকে সে সব দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে। তিন বাচ্চা নিয়ে মেতে আছে রোনাটা।
ডিনারের আসর জমিয়ে রাখল ব্রুনো একাই। নানান গল্পে, চুটকি রসিকতায়। রোনাটা বাচ্চাদের নিয়ে মেতে আছে, ক্লাউস-এর সঙ্গে ভালো করে কথা বলার সময়ই যেন নেই।
এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন দুজন পরিচিত ব্যক্তি-সস্ত্রীক ডক্টর স্কট এবং সিকিউরিটি অফিসার আর্নল্ড। খানাপিনা মিটতে বেশ রাত হল। বিদায় নিয়ে বের হবার সময় আর্নল্ড বলল, ডক্টর ফুকস্ আসুন আমার গাড়িতে। আপনাকে পৌঁছে দিয়ে যাই।
–চলুন।
গাড়িতে উঠে আর্নল্ড বললে, কেমন লাগল ওই ব্রুনো পরিবারকে?
–চমৎকার। ডক্টর ব্রুনো তো খুবই অমায়িক লোক। খুব হাসিখুশি, আমুদে। ভদ্রলোক এখানে চাকরি পেলে আমাদের জীবনযাত্রাটাই বদলে যাবে।
-তা হবার নয় ডক্টর। খুব সম্ভব ডক্টর ব্রুনো এখানে চাকরি পাবেন না।
–কেন? উনি তো নিজের বিষয়ে অত্যন্ত পণ্ডিত।
–পাণ্ডিত্যের জন্য আটকাবে না। ওঁর সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স পাওয়া শক্ত।
ক্লাউস ধমক দিয়ে ওঠে, ওই আপনাদের এক বাতিক। সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। সবাইকে শুধু সন্দেহ করেই জীবনটা গেল আপনাদের
-কী করব বলুন? এটাই তো আমাদের চাকরি। ডক্টর ব্রুনোকে চাকরি দেওয়ার মানে হয়তো আপনার মতো একজন নিরীহ বৈজ্ঞানিকের প্রাণ বিপন্ন করা।
–আমার? কেন, আমার প্রাণ বিপন্ন হতে যাবে কোন দুঃখে?
ধরুন দূর থেকে কেউ হয়তো একটা রাইফেল তাক করল ডক্টর ব্রুনোকে বধ করতে। লং রেঞ্জের রাইফেল। এবং গুলিটা আপনার সিটের আরও চোদ্দো ইঞ্চি ডাইনে সরে এসে বিধল। আপনাকে বাঁচাতে পারব তাহলে?
স্তম্ভিত হয়ে গেল ক্লাউস। বাক্যস্ফূর্তি হল না তার। আর্নল্ড নিজেই হেসে বলল, কই, নামুন এবার। আপনার বাসায় এসে গেছেন যে।
.
০৩.
ওই ঘটনার মাসখানেক পরে হঠাৎ মুক্তিপথের সন্ধান পেল ক্লাউস ফুকস। নতুন করে বাঁচবার একটা সম্ভাবনা দেখা দিল আচমকা। ওর বাবা প্যাস্টর এমিল ফুকস্ ওকে কিয়েল থেকে হঠাৎ একটা চিঠি লিখে এই নূতন জীবনের ইঙ্গিত পাঠিয়েছেন। ডক্টর এমিল ফুকসের বয়স তখন আশির কাছাকাছি। যুদ্ধ চলার সময় তিনি দীর্ঘদিন নাৎসি বন্দীশিবিরে কাটিয়েছেন। যুদ্ধান্তে মুক্তি পেয়ে চলে গেছেন কিয়েল-এ। এখন সেখানে চার্চের যাজক তিনি। এই কিয়েল-এই একসময় পড়ত ক্লাউস। বৃদ্ধ চিঠিতে জানিয়েছেন, কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টর ক্লাউস ফুকে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকপদে বরণ করতে ইচ্ছুক। সে যদি তার বর্তমান চাকরি ছেড়ে দেয় এবং ন্যাশনালিটি পরিবর্তন করতে রাজি থাকে তবে এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি পুত্রের কাছাকাছি থাকতে পারেন।
ক্লাউসের জীবনে ওই বৃদ্ধের অবদান অসামান্য। এই দুনিয়ায় সে যে-কজন মহাপুরুষকে শ্রদ্ধা করে তার অন্যতম তার জনক ওই পাদরি ফুক। সারা জীবন তিনি সংগ্রাম করে গিয়েছেন। একা হাতে। নাৎসি অত্যাচারের চুড়ান্ত হয়েছিল ওদের পরিবারে–যদিও ওরা ইহুদি ছিল না। ক্লাউসের মা সে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেন, ক্লাউসের ছোটোবোনও আত্মহত্যা করে। ক্লাউসের দাদা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তবু ঈশ্বরে বিশ্বাস হারাননি বৃদ্ধ। আজীবন একা হাতে লড়াই করে গেছেন। ক্লাউস নিজে জার্মানি থেকে পালিয়ে আসায় বৃদ্ধকে কোনোভাবেই সাহায্য করতে পারেনি। তাই বৃদ্ধ পিতার আহ্বানে সে বিচলিত হয়ে উঠল। বৃদ্ধ অবশ্য কিয়েলে একা থাকেন। মানুষ করেছেন ওঁর মা-হারা একমাত্র নাতিটিকে। ও যদি কিয়েলে গিয়ে অধ্যাপনা শুরু করে, সংসার পাতে, তাহলে ওই নাবালকটিরও ব্যবস্থা হয়। এ বিষয়েও ওই বৃদ্ধটি বিচলিত।
পিতৃদেবের চিঠিখানি নিয়ে সে গিয়ে দেখা করল হারওয়েলের সর্বময় কর্তা স্যার জনের সঙ্গে। স্যার জন বাস্তববাদী। সোজা কথার মানুষ। বললেন, হারওয়েলের তিন-নম্বরের চাকরির চেয়ে নিঃসন্দেহে কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের পদ আকর্ষণীয়। কিন্তু আরও একটা প্রশ্ন আছে। তুমি কি নিজের ন্যাশনালিটি বদলাতে প্রস্তুত? কিয়েল বর্তমানে রাশিয়ান গভর্নমেন্টের এক্তিয়ারে। কম্যুনিজমকে মেনে নিতে পারবে তো?
ভেবে দেখি–বলে ফিরে এসেছিল ক্লাউস।
এরপর দেখা করেছিল প্রফেসর কার্ল-এর সঙ্গে। রোনাটা খুব খুশি হয়েছে এমন ভাব দেখালো। বললে, নিশ্চয়ই নেবে এ চাকরি। প্যাস্টর ফুকসকে এই শেষ সময়ে কে দেখবে, তুমি ছাড়া? তাছাড়া ব-এর কথাটাও ভাবা দরকার। কিয়েলে গিয়ে সংসার পেতে বস। আর একটা কথা। বিয়ে কর এবার। তাহলে বব-এর একটা হিল্লে হয়ে যায়।
–আর আমি যদি বাবাকে লিখি ববকে এখানে পাঠিয়ে দিতে?
–তুমি মানুষ করতে পারবে? একা?
–কেন? তুমি তো আছ? ও তোমার কাছে থাকবে।
–দেবে আমাকে?-উৎসাহ উপচে পড়ে রোনাটার দু-চোখে। তারপরেই হঠাৎ সে কেমন বদলে যায়। বলে, কী স্বার্থপরের মতো কথা বলছি। তা কেন? তুমিই বরং কিয়েলে চলে যাও। সংসারী হও।
–প্রফেসর কার্ল কী পরামর্শ দেন?–ক্লাউস জিজ্ঞাসা করে।
–আমার আদৌ এতে সম্মতি নেই–প্রফেসর কার্ল-এর সাফ জবাব।
–কেন?
–সেটা পরে তোমাকে বলব।
রোনাটা চট করে উঠে দাঁড়ায়। বলে, পরে কেন? এখনই বল; আমি চলে যাচ্ছি।
-না না, তা বলিনি আমি।–প্রফেসর বিব্রত হয়ে ওঠেন।
রোনাটাও হেসে হালকা করে পরিবেশটা। বলে, না, রাগ করে উঠে যাচ্ছি না। কফি করে আনি।
প্রফেসর কার্ল তৎক্ষণাৎ বলেন, ক্লাউস, তুমি ডক্টর কাপিৎজার নাম শুনেছ? ফুঁ হেসে বলে, স্যার দুনিয়ার এমন কোনো নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট আছে যে, লর্ড রাদারফোর্ডের শ্রেষ্ঠ ছাত্রটির নাম শোনেনি।
–তিনি এখন কোথায় জান?
–ঠিক জানি না। আন্দাজ করতে পারি। মস্কো অথবা লেনিনগ্রাডে–কিয়েলেও হতে পারেন। ডক্টর কাপিৎজা আজকের রাশিয়ার সবচেয়ে বড় নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট।
তোমার দ্বিতীয় বক্তব্যটা ঠিক, প্রথমটা নয়। ডক্টর কাপিৎজা বর্তমানে আছেন সাইবেরিয়ায়। বন্দীজীবন যাপন করছেন তিনি। তার অপরাধ, স্তালিনের হুকুমে তিনি অ্যাটম-বোমা বানাতে অস্বীকার করেছিলেন। বলেছিলেন এজন্য লর্ড রাদারফোর্ড প্রোটন আবিষ্কার করেননি।
বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় ক্লাউস। অস্ফুটে বলে, আমি বিশ্বাস করি না। কী করে জানলেন?
-কী করে জানলাম সেটা বলব না। তবে আমার কথা অভ্রান্ত সত্য বলে মেনে নাও।
ডক্টর কাপিৎজা ছিলেন লর্ড রাদারফোর্ড-এর ডান হাত। কেমব্রিজ বীক্ষণাগারে রাদারফোর্ড-এর তখন তিনজন শিষ্য প্রতিভার স্বাক্ষরে ভাস্বর–কাপিজা, চ্যাডউইক আর অটো কার্ল। সে হিসাবে প্রফেসর কার্ল হচ্ছেন কাপিজার সতীর্থ। এর মধ্যে কাপিজার সম্ভাবনাই ছিল সবচেয়ে বেশি। যদিও বাস্তবে চ্যাডউইকই সবচেয়ে নাম করেছেন–নিউট্রন আবিষ্কার করে নোবেল লরিয়েট হয়েছেন।
কাপিৎজা ছিলেন প্রাণবন্ত, উচ্ছল! রাদারফোর্ড-এর সবচেয়ে প্রিয় ছাত্র। রাদারফোর্ড ছাত্রকে একটি সুন্দর ল্যাবরেটরি বানিয়ে দিয়েছিলেন। কাপিৎজা সেই ল্যাবরেটারির প্রবেশপথে বসিয়েছিলেন একটি মর্মরমূর্তি–বিখ্যাত ইংরেজ ভাস্কর এরিক গিলকে দিয়ে। একটি কুমিরের মূর্তি! কুমির কেন? সাংবাদিকরা প্রশ্ন করল দ্বারোদ্বাটনের দিন। কাপিৎজা গম্ভীর হয়ে বললেন–’কুমীর কখনও ঘাড় ঘোরাতে পারে না। সে সিধে সামনের দিকে চলে। সেই হচ্ছে আমার বিজ্ঞান-সাধনার প্রতীক।‘
সাংবাদিকরা অবাক হয়। প্রফেসর রাদারফোর্ড তাদের জনান্তিকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন–আমার ছাত্রটির মাথায় দু-চারটে স্ক্রু আলগা।
এবার সাংবাদিকেরা হেসেছিল।
হেসেছিল কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাও। মুখ লুকিয়ে। তারা জানত, জনান্তিকে কাপিৎজা রাদারফোর্ড-এর নতুন নামকরণ করেছে-’কুমীর-সাহেব। রাদারফোর্ড তা জানতেন না, কিন্তু ল্যাবরেটারির বেয়ারাটা পর্যন্ত জানত এ গুপ্তরহস্য। কাপিজা তাই তার বিজ্ঞানমন্দিরে বসিয়েছে কুমীরের মূর্তি-গুরুদক্ষিণা।
নতুন ল্যাবরেটারির উদ্বোধন হল 1933-এ। ঠিক তার পরেই রাশিয়া থেকে একটি আমন্ত্রণ পেয়ে কাপিৎজা গেল স্বদেশে। মক্সো বিজ্ঞান-অধিবেশনে যোগ দিতে। সেটাই হল ওর সর্বনাশের সূত্রপাত। ফিরে আসতে দেওয়া হলনা কাপিৎজাকে। স্তালিন জানালেন, অতঃপর ওকে রাশিয়াতে থেকেই বিজ্ঞানচর্চা করতে হবে। কাপিজ্জা নিজের জন্মভূমিতে অন্তরীণ হল। গোপনে সে খবর পাঠালো রাদারফোর্ডের কাছে–জানালো, সে কেমব্রিজে ফিরে আসতে চায়। তার নতুন ল্যাবরেটারিতে। লর্ড রাদারফোর্ড মস্কোর কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি লিখলেন। তার ছাত্রকে ফিরে আসতে দেবার অনুমতি দেওয়া হোক। রাশিয়ান সরকার প্রত্যুত্তরে লিখল-ইংল্যান্ডের পক্ষে একথা লেখা খুবই স্বাভাবিক। তারা খুশি হবে কাপিৎজা যদি কেমব্রিজে গবেষণা করেন। অনুরূপভাবে আমরাও খুশি হব, যদি লর্ড রাদারফোর্ড মস্কোতে এসে গবেষণা করেন।
রাদারফোর্ড এরপর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বল্ডউইনের দ্বারস্থ হলেন। লর্ড রাদারফোর্ডের অনুরোধে বল্ডউইন সরকারি পর্যায়ে এ অনুরোধ জানালেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। কাপিৎজার এক আত্মীয়া লন্ডনে সোভিয়েত এম্বাসিতে গিয়ে স্বয়ং অ্যাম্বাসাডারকে নাকি বলেছিলেন, এভাবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাপিজাকে আপনারা কিছুতেই আটকে রাখতে পারবেন না। ওর মাথা পাথরের মতো শক্ত। বুঝেছেন?
রাশিয়ান রাষ্ট্রদূত নাকি জবাবে হেসে বলেছিলেন, ফর য়োর ইনফরমেশন ম্যাডাম, জোসেফ স্তালিনের মাথাটাও জেলির মতো নয়।
রাদারফোর্ডকে লেখা কাপিজার শেষ চিঠিটায় (1933) ছিল একটা বিজ্ঞানোত্তর দার্শনিক তত্ত্ব : After all, we are only small particles of floating matter in a stream which we call Fate. All that we can manage is to deflect our tracks slightly and keep afloat–the stream governs us.
[যত যাই বলুন, আমরা প্রবহমান খরস্রোতে ভাসমান তৃণখণ্ড বইতো নই? ওই স্রোতটারই অপর নাম নিয়তি। বড় জোর খড়কুটোর মতো একটু এপাশ-ওপাশ সরে-নড়ে বেড়াতে পারি, কোনোক্রমে ভেসে থাকতে পারি–আমাদের গতি নিয়ন্ত্রিত হবে ওই স্রোতেরই নির্দেশে।]
এরপর রাদারফোর্ড যা করে বসলেন তা তার মতো আত্মভোলা বৈজ্ঞানিকের পক্ষেই শুধু সম্ভব। তিনি কাপিৎজার জন্য তৈরি সদ্যসমাপ্ত ল্যাবরেটারির সব যন্ত্রপাতি খুলে ফেললেন। বড় বড় ক্রেটে সমস্ত যন্ত্রপাতি ভরে পাঠিয়ে দিলেন মস্কোতে। রাশিয়ান সরকারকে লিখলেন–কাপিৎজার সঙ্গে কেমব্রিজ ল্যাবরেটারির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। এটা রাজনীতির কথা নয়, বিজ্ঞানের হিসাব! ও আপনারা বুঝবেন না। তাই কাপিজা যখন কেমব্রিজে আসতে পারল না, তখন কেমব্রিজই তার কাছে যাক।
এমনকি তিনি জাহাজে করে পাঠিয়ে দিলেন সেই পাথরের কুম্ভীর মূর্তিটাকেও।
মস্কোর সোনার খাঁচায় ময়না ‘রাধাকৃষ্ণ’ পড়েছিল কিনা পশ্চিম দুনিয়া সেকথা জানতে পারেনি।
এরপর লৌহ যবনিকার এপারে বহির্বিশ্বে কাপিৎজার কণ্ঠস্বর মাত্র একবার শোনা গিয়েছিল। 1946-এ। বিকিনি অ্যাটলে যখন আমেরিকা থার্মোনিউক্লিয়ার বোমার বিস্ফোরণ ঘটালো তখন কাপিৎজার একটা বাণী কেমন করে জানি লৌহ যবনিকা ভেদ করে এপারে আসে। কাপিৎজা বলেছিলেন :
“To speak about atomic energy in terms of atomic bomb is comparable with speaking about electricity in terms of electric chair.”
[পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগ হিসাবে যাঁরা পারমাণবিক-বোমার কথাই শুধু চিন্তা করতে পারেন, তারা বোধকরি বিদ্যুৎ-শক্তির প্রয়োগ-হিসাবে শুধু ইলেকট্রিক চেয়ারের কথাই ভাবেন।]
***
অনেক পরে জানা গেছে কাপিৎজা সোভিয়েত সরকারের নির্দেশে বেশ কিছুদিন তার বিজ্ঞানমন্দিরে কাজ করেন। সরকারের সঙ্গে তাঁর প্রথম বিরোধ বাধল যখন নির্দেশ এল এবার পরমাণু-বোমা বানাতে হবে। বিরোধ ঘনীভূত হল; কারণ কাপিৎজা অস্বীকৃত হলেন। তার চাকরি যায়। ওই বিজ্ঞানমন্দিরে প্রবেশের অধিকার খোয়ালেন কাপিৎজা। এরপর গৃহবন্দীর জীবন। তবু স্তালিনের প্রস্তাবে স্বীকৃত হলেন না তিনি। তাঁর সাফ জবাব–এজন্য তার গুরু রাদারফোর্ড অথবা গুরুভাই চ্যাডউইক পরমাণুর হৃদয় বিদীর্ণ করেননি। বলেছিলেন, ওই উদ্দেশ্যে পরমাণুর হৃদয় বিদীর্ণ করার আগে আমি নিজের হৃৎপিণ্ডটা বিদীর্ণ করব।
স্তালিনের আদেশে কাপিৎজাকে নির্বাসনে পাঠানো হল। টেস্টটিউব, ব্যুরেট আর সাইক্লোট্রোন নিয়ে যাঁর জীবন কেটেছে এবার তার হাতে তুলে দেওয়া হল গাইতা আর হাতুড়ি। সশ্রম কারাদণ্ড। সাইবেরিয়ায়।
কাপিৎজার সমাধি কোথায় কেউ জানে না।
..দীর্ঘ কাহিনি শেষ করে প্রফেসর কার্ল বলেন, আই হেট দিজ কম্যুনিস্ট। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ তুমি কিয়েল-এ চলে যেও না। তার চেয়ে অনেক-অনেক ভালো হারওয়েলের এই তিন নম্বর চাকরি। এখানে আমরা মানুষের কল্যাণের জন্য প্রাণপাত করছি। স্যার জন তো এ বছরেই অবসর নিচ্ছেন। আমি আর কদিন? হয়তো তিন-চার বছরের ভিতরেই তুমি এখানকার কর্ণধার হয়ে বসবে। তা ছাড়া
বাধা দিয়ে ক্লাউস বলে, প্রফেসর, আপনি কাপিৎজার সম্বন্ধে এত খবর পেলেন কোথায়?
প্রফেসর কার্ল একটু বিব্রত হয়ে বলেন, সে যেখান থেকেই পাই।
তবু বলুন না?
–না। বলায় বাধা আছে। তবে যা বলছি তা নিছক সত্য।
–আপনি শুনেছেন একপক্ষের কথা। সোভিয়েত-বিরোধীদের প্রচার।
–না না। আই হ্যাভ হার্ড ইট ফ্রম দ্য হর্সেস মাউথ। খাঁটি লোকের মুখ থেকে।
–কিন্তু কে সেই খাঁটি লোক?
–বলছি তো–তা বলা চলে না তোমাকে।–প্রায় ধমকের সুরে বলেন উনি।
ক্লাউস চুপ করে যায়। প্রফেসরও একটু বিব্রত হয়ে পড়েন। একেবারে অন্য সুরে বলেন, তার চেয়ে তুমি তোমার বোনপো বব-কে নিয়ে এস। সে আমাদের পরিবারেই থাকবে। রোনাটার একটা অবলম্বন হবে। আর তাছাড়া…
আবার চুপ করে যান। ইতস্তত করেন। শেষ পর্যন্ত মনের দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বলেন, তুমি চলে গেলে ও একেবারে মুষড়ে পড়বে। ও তোমাকে খুব ভালোবাসে।
ঠিক সেই মুহূর্তেই কফির ট্রে হাতে নিয়ে এ ঘরে আসছিল রোনাটা। কথাটা কানে গেল তার। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। আর এ ঘরে এল না। পর্দা সরিয়ে একটু পরে রোনাটার মেড-সার্ভেন্ট ডরোথি কফির ট্রে নিয়ে প্রবেশ করল। সেদিন আর রোনাটা ওদের সামনে আদৌ এসে দাঁড়াতে পারেনি।
কিন্তু দিনতিনেক পরে সে এসে দাঁড়ালো ফুকস-এর মুখোমুখি। জনান্তিকে। বলল, প্লিজ ক্লাউস, তুমি ওই চাকরি নিয়ে কিয়েল চলে যাও।
ক্লাউস অবাক হয়। বলে, কেন বলতো? তোমার গরজ কী?
রোনাটার কণ্ঠস্বর একটুও কাঁপল না। সে স্পষ্ট গলায় পরিষ্কার ভাষায় বললে, তুমি বুঝতে পার না? আমি আর সহ্য করতে পারছি না। তোমার দূরে চলে যাওয়াই মঙ্গল। তোমাকে আমি ভুলতে চাই। তোমাকে…তোমাকে আর সহ্য করতে পারছি না আমি।
কী জবাব দেবে বুঝে উঠতে পারে না ক্লাউস। চট করে সে উঠে দাঁড়ায়। হ্যাট-র্যাক থেকে টুপিটা নিয়ে বলল, চলি।
তারপর দরজা কাছ পর্যন্ত এগিয়ে বললে, তুমি আজ উত্তেজিত। না হলে আমিও মন খুলে দু-একটা কথা বলতাম।
শান্ত সমাহিত স্বরে রোনাটা বললে, কেন? আমাকে কি উত্তেজিত মনে হচ্ছে?
–হ্যাঁ। তুমি জোর করে তোমার উত্তেজনা ঢেকে রেখেছ।
-মোটেই নয়। তোমার কিছু বলার থাকলে স্বচ্ছন্দে বলতে পার। আমি প্রস্তুত।
ক্লাউস ফিরে এসে বসে তার চেয়ারে। বলে, সব কথা প্রফেসরকে খুলে বললে কেমন হয়?
–সব কথা মানে?
-তুমি তাকে ডিভোর্স করতে চাও। আমি তোমাকে বিবাহ করতে চাই। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়ায় রোনাটা। মুখখানা সাদা হয়ে যায় তার। ঠোঁট দুটো নড়ে ওঠে। তারপর সে অসীম বলে আত্মসম্বরণ করে। স্পষ্টভাবে বলে, এ কথা আর কোনোদিন উচ্চারণ কোরো না।
ধীরপদে চলে যাবার জন্যে পা বাড়ায়। ক্লাউস পিছন থেকে বলে, কারণটা বলে যাবে না?
দ্বারের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ে রোনাটা। বলে, প্রয়োজন ছিল না। দশ বছর আগে কারণটা তুমিও বলেনি। তবে প্রশ্ন যখন করলে তখন আমি কারণটা জানাব। আমি মনে-প্রাণে রোমান ক্যাথলিক। বিবাহ আমার কাছে ইন্দ্রিয় ব্যভিচারের একটা পাসপোর্ট নয়। তুমি যা ভাবছ তা নয়। প্রফেসরকে আমি ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি–ঠিক যতটা আমার বাবাকে ভালোবাসতাম।
ক্লাউস আরও কিছু কথা বলতে চায়; কিন্তু তাকে থামিয়ে দেয় রোনাটা : আমার মনে হয়, এর পর তোমার এ বাড়িতে না আসাই মঙ্গল।
.
০৪.
হারওয়েলে ব্রুনো পন্টিকার্ভোর চাকরি শেষ পর্যন্ত হল না, প্রফেসর কার্লের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও। তবু একটা ব্যবস্থা হল, প্রফেসর কার্ল-এর সুপারিশেই। লিভারপুল ইনস্টিক্ট ওকে একটা ভালো চাকরির অফার দিল। পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রে নয়, পদার্থবিজ্ঞানীর মামুলি কাজ। তবে মাইনেটা ভালো। ব্রুনো এককথায় রাজি হল। ধন্যবাদ জানালো প্রফেসরকে। তৎক্ষণাৎ সে লিভারপুল কর্তৃপক্ষকে জানালো অনতিবিলম্বেই সে ওই চাকরিতে যোগ দেবে। তবে তার আগে সে একবার ইটালিতে যেতে চায়। মিলানে আছেন তার বৃদ্ধ পিতামাতা। যুদ্ধান্তে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। ওই সঙ্গে সে একবার সুইডেনেও যেতে চায় সস্ত্রীক। সুইডেন-এর রাজধানী স্টকহম হচ্ছে ব্রুনোর শ্বশুরবাড়ি। সেখানে আছেন ফ্রাই পন্টিকোর্ভোর পিতা মিস্টার নর্ডব্লম এবং তাঁর স্ত্রী। দিন-পনেরোর ব্যাপার। এ ছাড়া সুইজারল্যান্ডের শ্যামনীতে একটি বিজ্ঞান-কংগ্রেস থেকে সে আমন্ত্রণ পেয়েছে। সেখানেও যেতে হবে ফেরার পথে। সব মিলিয়ে প্রায় তিন সপ্তাহ। লিভারপুল কর্তৃপক্ষ রাজি হলেন। চাকরিটা তারা মাসখানেক খালি রাখবেন। ব্রুনো কন্টিনেন্ট যাবার জন্য তৈরি হয়।
আর্নল্ড ইতিপূর্বেহ খবর পেয়েছে, ব্রুনো পন্টিকার্ভো একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোনো প্রত্যক্ষ অভিযোগ নেই। কোনো প্রমাণ নেই। ব্রুনো ন্যাচারালাইজড ব্রিটিশ প্রজা। ইটালিতে তার বাবা-মা এবং সুইডেনে শ্বশুর-শাশুড়ি আছেন। ইয়োরোপে ভ্রমণের পাসপোের্টও আছে তার, আছে ওইসব দেশের ভিসা। তাকে আটকানোর কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তাছাড়া সে তো কিছু পালিয়ে যাচ্ছে না, যাচ্ছে মাত্র এক মাসের জন্য। তার টিকি বাঁধা আছে। লিভারপুলে। হুঁ হুঁ বাবা! চাকরি বলে কথা।
অধ্যাপক কার্ল ব্রুনোর জন্য একটি বিদায় ভোজের আয়োজন করলেন। ব্রুনো আপত্তি করেছিল। বলেছিল, আমি তো মাত্র এক মাসের জন্যে যাচ্ছি প্রফেসর। বিদায় ভোজ কীসের?
-তা কেন? তুমি তো হারওয়েলে আর ফিরছ না। ফিরছ লিভারপুলে।
–তা বটে।
এই বিদায় ভোজে ঘটল পর পর দুটো ঘটনা যাতে চঞ্চল হয়ে উঠল আর্নল্ড। প্রথম ঘটনা ঘটল টেনিস-কোর্টে।
ব্রুনো খুব ভালো টেনিস খেলত। য়ুনিভার্সিটিতে সে বহুবার কাপ-মেডেল পেয়েছে। এমনকি যুদ্ধের সময় কানাডাতে চক-রিভারে যখন অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনে চাকরি করত তখনও ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়নশিপে সে প্রথম হয়েছিল। বিদায় ভোজের সন্ধ্যায় খেলার আয়োজন হল। শেষ গেমটা খেললেন মিসেস সেলিগম্যান আর ব্রুনো। ব্রুনোই জিতল। প্যাভেলিয়নে ফেরার পথে–ব্রুনো হঠাৎ বললে, কে বলতে পারে, আবার হয়তো একদিন আমরা খেলব। সেদিন আপনি জিতবেন।
মিসেস সেলিগম্যান থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। বলেন, মানে? আমরা তো আবার খেলব নিশ্চয়ই। একমাস পরেই। আপনি এমনভাবে বললেন কথাটা!
উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠে ব্রুনো। সামলে নিয়ে বলে, এসব কথা একটু রোম্যান্টিক গলায় বললেই শুনতে ভালো লাগে না কি?
ততক্ষণে মিসেস সেলিগম্যানও হেসে ফেলেন।
দ্বিতীয় ঘটনা ঘটল রাত্রে খাবার সময়। সবাই যখন আনন্দ উৎসবে মগ্ন তখন রোনাটার হঠাৎ খেয়াল হল, হেলেনা খানাকামরায় নেই। রোনাটা একটু অবাক হয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে বারান্দায়। সেখানেও হেলেনা নেই। একটু খোঁজ করতেই দেখা গেল হেলেনা নিজের ঘরে চুপ করে বসে আছে। তার চোখ দুটো ভেজা।
-তুমি এখানে?
মুহূর্তে হেলেনা নিজেকে সামলে নেয়। রুমালে মুখটা মুছে নিয়ে বললে, কিছু নয়, চল ওঘরে যাই।
ঘটনাটা সামান্য। তবুও অদ্ভুত। মিসেস ব্রুনো যাচ্ছে বেড়াতে-ইটালি আর সুইডেনে। তাহলে?
***
পঁচিশে জুলাই ওরা রওনা হয়ে গেল। ডানকার্ক হয়ে প্রথম যাবে সুইজারল্যান্ডে। সেখান থেকে ইটালি। ওরা যেদিন রওনা হয়ে গেল ঠিক তার পরের দিন, ছাব্বিশ তারিখে, আর্নল্ডের কাছে এসে পৌঁছালো একটা কেবলগ্রাম। সুদূর মার্কিন মুলুক থেকে। কোড মেসেজে এফ. বি. আই. স্কটল্যান্ড-ইয়ার্ডকে জানাচ্ছে : অনুমান করার যথেষ্ট কারণ দেখা যাচ্ছে যে, ব্রুনো পন্টিকার্ভোই আসলে ডগলাস। তাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করুন। প্রমাণাদি পাঠাচ্ছি।
এ তারবার্তা যখন এসে পৌঁছালো তখন ব্রুনো সপরিবারে চলেছে। সুইজারল্যান্ড ছেড়ে ইটালির দিকে। একটু ঘুরপথে দেশ দেখতে দেখতেই যাচ্ছে। ব্যস্ততা কী? তাকে তো আর বাঘে তাড়া করেনি। অস্ট্রিয়ার ইনস্বার্গের কাছাকাছি এসে ‘ইন’ নদীর অববাহিকা ধরে চলেছে সে ব্রেনার পাস্-এর দিকে, যেখানে এককালে ইউরোপ-কেক কাটার প্ল্যান করতে বসেছিলেন হিটলার আর মুসোলিনি! স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের অভিজ্ঞ গোয়েন্দা স্কার্ডন রওনা হয়ে গেল প্লেনে। ব্রুনো ক্রমাগত দেশ থেকে দেশান্তরে যাচ্ছে। বিদেশে তাকে গ্রেপ্তার করা সহজ নয়। বিদেশে তাকে গ্রেপ্তার করতে হলে সে দেশের অনুমতি চাই। তবে ব্যস্ত হবার কিছু নেই–ব্রুনোর জন্য খাঁচা বানানো হয়েছে লিভারপুলে। পাখি খাঁচায় ফিরে আসবেই। তখনই ঝাঁপ বন্ধ করতে হবে। স্কার্ডন-এর ওপর আদেশ ছিল শুধু নজর রেখ সে যেন সাম্যবাদ-ঘেঁষা কোনো দেশে না যায়। অবশ্য সে সব দেশে যাওয়ার ছাড়পত্রও ছিল না ব্রুনোর পাসপোর্টে।
ব্রুনো সপরিবারে মিলানে এসে পৌঁছলো বারোই আগস্ট। বাবা-মার সঙ্গে দেখা করল। মিলানের দ্রষ্টব্য জিনিসগুলি দেখাল স্ত্রীকে। স্কালা, মিলান-গির্জা, লেঅনার্দোর লাস্ট সাপার। জেমস্ স্কার্ডন এখানেই তার সন্ধান পায়। টুরিস্টের বেশে সে বরাবরই ছিল কাছে কাছে। এরপর ব্রুনো চলে যায় সিসেরোতে। সেখানে বাইশে আগস্ট স্কার্ডন দেখল কী একটা উৎসব হচ্ছে। কী ব্যাপার? শোনা গেল, ব্যাপার এমন কিছু গুরুতর নয়, ব্রুনো পন্টিকার্ভোর সেটা সাঁইত্রিশতম জন্মদিন। তার পর দিন ওরা চলে এল রোমে। ছায়ার মতো অনুসরণ করে চলেছে স্কার্ডন। তবে বারে বারে ভোল পালটাচ্ছে। মিলানে সে ছিল আমেরিকান টুরিস্ট–চোখে চশমা, দাড়ি-গোঁফ কামানো। রোমে সে হচ্ছে ফরাসি চিত্রকর। একমাথা চুল, একমুখ দাড়ি, চোখে গগল্স, হাতে রং-তুলি, ঈজেলের ব্যাগ। ব্রুনো অথবা হেলেনা যেন লক্ষ্য না করে একজন তোক ক্রমাগত তাদের পেছন পেছন। ঘুরছে–মিলান থেকে সিসেরো, সেখান থেকে রোম।
***
উনত্রিশে আগস্ট ব্রুনো সস্ত্রীক রোমের সিটি অফিসে এল একদিন। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান এয়ারওয়েজ-এর বুকিং কাউন্টারে। সেখানে গিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল সুইডেন-এর রাজধানী স্টকমে যাওয়ার ভাড়া কত। ব্রুনো নিশ্চয় খেয়াল করেনি, কিউ-সরীসৃপে ঠিক ওর পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল একজন ফরাসি আর্টিস্ট। চাপ দাড়ি, চোখে গগস, মাথায় বাউলার হ্যাট। বুকিং ক্লার্ক কী জবাব দিল তা। শুনতে পেল না স্কার্ডন। কিন্তু দেখল ব্রুনো তার ওয়ালেট খুলে নোট বার করছে। ঠিক এই সময় হেলেনা তার স্বামীর জামার হাতটা ধরে টানল। কী যেন বলল, জনান্তিকে। ব্রুনো লাইন ছেড়ে একটু দূরে সরে গেল। স্বামী-স্ত্রীতে কী জাতীয় জনান্তিক আলাপচারিতা হল তাও শুনতে পেল না স্কার্ডন। কিউ-সরীসৃপে স্কৰ্ডনের পিছনে যে ছিল সে তাকে একটা কুনুইয়ের গোঁত্তা মেরে বললে, ততক্ষণ আপনি টিকিটটা কেটে ফেলুন না মশাই? ওঁদের দাম্পত্যসম্ভাষণ শেষ হতে হতে কাউন্টার বন্ধ হয়ে যাবে।
স্কার্ডন আর কোনমুখে বলে–তা কি পারি স্যার? উনি যখন যেখানে যাবেন তখন সেখানেই যে যাব আমি। সে বরং ভাব দেখায় যেন ভদ্রলোকের কথা আদৌ বুঝতে পারছে না। তা তো হতেই পারে–সে ফরাসি আর্টিস্ট, ইটালিয়ান ভাষা সে জানে না। পেছনের লোকটি তখন ওকে গোঁত্তা মেরে সরিয়ে দেয়। ভাষা না বুঝলেও গোঁত্তা সবাই বোঝে। স্কার্ডন সরে আসে। ভদ্রলোক তখন তার টিকিট কাটে। ইতিমধ্যে কথাবার্তা সেরে ব্রুনো ফিরে এল কাউন্টারে। বললো, চারখানা স্টকহমের টিকিট দিন। টুরিস্ট ক্লাস। আমার, স্ত্রীর আর বাচ্চাদের। আমারটা হবে রিটার্ন টিকিট।
হিসাব করে কাউন্টারের লোকটা বললে, সবশুদ্ধ ছয়শ দুই ডলার।
ব্রুনো তার ব্যাগ খুলে সাতখানা কড়কড়ে একশ ডলারের নোট বার করে। লোকটা বললে, দু ডলার খুচরো দিন।
ওয়ালেট হাতড়ে ব্রুনো বললে, দুঃখিত। খুচরো নেই।
কথাবার্তা আদ্যন্ত হচ্ছিল ইটালিয়ান ভাষায়। ফরাসি চিত্রকরটির বোঝার কথা নয়। কিন্তু সে মনে মনে হাসল। দুটি ব্যাপারে খুশি হয়েছে সে। প্রথমত, ব্রুনো নিজের টিকিট রিটার্ন কাটল। দ্বিতীয়ত, বেশ বোঝা যাচ্ছে সে কোনো সূত্র থেকে ডলার পাচ্ছে। অঢেল টাকার মালিক-আমেরিকান টুরিস্ট ছাড়া সচরাচর এমন একশ ডলারের করকরে নোট কেউ বার করে না। ভাঙানি আটানব্বই ডলার নিয়ে ব্রুনো চলে যেতেই স্কার্ডন এগিয়ে এল কাউন্টারে। টিকিট কাটল। স্টকহমের। একই দিনের। একই প্লেনের।
পয়লা সেপ্টেম্বর এস. এ. এস. প্লেনে মিউনিক-কোপেনহেগেন হয়ে সপরিবারে ব্রুনো এসে পৌঁছালো স্টকহমে। প্লেন থেকে নেমে এয়ার-টার্মিনালে এল ওরা। ছায়েবানুগত যথারীতি ফরাসি চিত্রকর ভদ্রলোকও। মালপত্রগুলি তখনও এসে পৌঁছায়নি। ব্রুনো ট্যাগ হাতে মালের জন্য প্রতীক্ষা করছে। স্কার্ডন ওর হাত থেকে হাত- তিনেক দূরে একটা বুকস্টলে দাঁড়িয়ে অন্যদিকে ফিরে সিগারেট খাচ্ছে আর ফরাসি ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছে। হঠাৎ একটা কথায় চমকে উঠল স্কার্ডন। ব্রুনোর বড় ছেলে ইটালিয়ান ভাষায় প্রশ্ন করল, মাম্মি! এটাই কি রাশিয়া!
ব্রুনো হঠাৎ ধমক দিয়ে উঠল, বকবক কর না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক।
স্কার্ডন তখন মনে মনে ভাবছে ওর চমকটা কি লক্ষ্য করেছে ব্রুনো? নিশ্চয় নয়। সে তো এক-সেকেন্ডের দশভাগের একভাগ সময় মাত্র চমকে চোখ তুলে তাকিয়েছে ওর ছেলের দিকে। ব্রুনো নিজেও নিশ্চয় চমকে উঠেছিল। সে খেয়াল করবে না। তাছাড়া ব্রুনো স্কার্ডনকে হারওয়েলে কোনোদিন দেখেনি। তার ওপর সে ছদ্মবেশে আছে। সর্বোপরি সে বর্তমানে ফরাসি চিত্রকর, ইটালিয়ান ভাষা জানে না। ফলে ব্রুনো নিশ্চয়ই আতঙ্কিত হবে না।
হেলেনা তার স্বামীকে বললে, এয়ারপোর্ট থেকেই সোজা বাবার ওখানে চলে। যাই না কেন?
ব্রুনো বললে, সেটা ভালো দেখায় না। আমি ওইজন্যে হোটেল কঁতিনেতালে আগে থেকেই ঘর বুক করে রেখেছি। হোটেলে পৌঁছে তোমার বাবাকে ফোন করব।
স্কার্ডন পাকা গোয়েন্দা। কোনো ফাঁদে পা দিতে সে প্রস্তুত নয়। সে তৎক্ষণাৎ সরে যায় ‘ওয়েটিং হল’-এর অপরপ্রান্তে। পাবলিক টেলিফোন বুথে ঢুকে পড়ে। কাঁচের ঘর। ওখান থেকে ব্রুনো পরিবারকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নজর এড়াচ্ছে না। গাইড হাতড়ে বার করে হোটেল কঁতিনেতাল-এর নম্বর। ডায়াল করে সেই নম্বরে। রিসেপশান ধরতেই বললে, একটু দেখে বলুন তো ডক্টর ব্রুনো পন্টিকার্ভোর নামে ঘর বুক করা আছে কিনা।
ওপ্রান্তে সুকণ্ঠী মহিলাটি বললেন, আছে। আপনিই কি ডক্টর পন্টিকার্ভো?
-না না। আমি ওঁর একজন বন্ধু। তার সঙ্গে ওখানে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। যাই হোক রুম নম্বরটা কত?
–825 এবং 126।
–ধন্যবাদ।
এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ও বেরিয়ে আসে পথে। তখনও ব্রুনোর মালপত্র প্লেনের গর্ভ থেকে ওখানে এসে পৌঁছায়নি। একটা ট্যাক্সি নিল স্কার্ডন। বললে, হোটেল কঁতিনেতাল।
ওখানেই উঠল সে। আটতলাতেই ঘর পেল। 811। এটা 826-এর ঠিক উল্টোদিকে এবং রাস্তার দিকে। মালপত্র নিয়ে ঘরে চলে গেল স্কার্ডন। ঘরটা বন্ধ। করে গিয়ে বসল জানলার ধারে। যেখানে বসে হোটেলের প্রবেশপথটা দেখা যায়। সুটকেস থেকে বাইনোকুলারটা বার করল। যতক্ষণ ব্রুনো পরিবার হোটেলে এসে
পৌঁছাচ্ছে ততক্ষণ ও নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। অবশ্য চিন্তা করার কিছু নেই। এখানেই ঘর রিজার্ভ করা আছে তার। ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করে কেমন যেন। সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ে স্কার্ডন। ব্যাপার কী? ঘরে তালা মেরে সে নেমে এল রিসেপশানে। কাউন্টারে যে মেয়েটি ছিল তাকে প্রশ্ন করে, ডক্টর ব্রুনো পন্টিকার্ভোর নামে কোনো রিজার্ভেশান আছে?
মেয়েটি একটি রেজিস্টার দেখে বললে, আছে। দুখানা ঘর। নাম্বার 825 এবং 826। আজই তার আসার কথা। এয়ারপোর্ট থেকে তিনি ফোনও করেছেন। এখনই আসছেন বললেন।
–ধন্যবাদ। আচ্ছা কতক্ষণ আগে তিনি ফোন করেছেন বলুন তো?
–ধরুন ঘণ্টাখানেক আগে।
–ডক্টর ব্রুনো কি নিজেই ফোন করেছিলেন? না তার বন্ধু?
বন্ধু আগে করেছিলেন। তার মিনিট পনেরো পরে ডক্টর নিজেই ফোন করেন।
স্কার্ডন নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের ঘরে ফিরে এল।
কিন্তু একী! আরও ঘণ্টা দুই কেটে গেল। ব্রুনো এলো না। এবার আর। কাউন্টারে গিয়ে খোঁজ নিতে সাহস হল না। বেশি কৌতূহলী হলে চিহ্নিত হয়ে পড়বে। ফোন করল পরপর 825 এবং 826 নং ঘরে। দু জায়গাতেই ফোন বেজে গেল। কেউ ধরল না। অর্থাৎ ওর নজর এড়িয়ে কোনো অসতর্ক মুহূর্তে ব্রুনো পরিবার আসেনি। এতক্ষণে একটু নার্ভাস হয়ে পড়েছে স্কার্ডন। চাকরির রেকর্ডে তার দাগ পড়েনি ইতিপূর্বে। এমন হাতের মুঠো থেকে শিকার ফসকালে সে মুখ দেখাবে কী করে? কিন্তু ওরা যাবে কোথায়? তবে নিশ্চয় মিসেস ব্রুনোর পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত মত বদলেছে ব্রুনো। সোজা চলে গেছে শ্বশুরবাড়ি। এমনও হতে পারে ওর শ্বশুর এয়ারপোর্টে গিয়েছিলেন। দেখা হয়ে গেছে। মেয়ে-জামাইকে পাকড়াও করে নিয়ে গেছেন। এইটেই একমাত্র সমাধান। স্কার্ডন ঘড়ির দিকে তাকায়–রাত এগারোটা। অর্থাৎ ইতিমধ্যে চারঘণ্টা হয়ে গেছে। টেলিফোন ডাইরেক্টারি হাতড়ে বার করল একটা নম্বর। ডায়াল করল। মহিলাকণ্ঠে কেউ বললেন, হ্যালো!
ইটালিয়ান ভাষায় স্কার্ডন বলে, মিস্টার নর্ডব্লম-এর বাড়ি?
–হ্যাঁ। মিসেস নর্ডব্লম বলছি। কাকে চান?
–দেখুন, আপনি আমাকে চিনবেন না। আমি ডক্টর ব্রুনোর একজন বন্ধু। সে আমাকে লিখেছে আজ সে এখানে আসবে–
–আমরাও তো তাই জানি। ব্রুনো একা নয়। তার সপরিবারে আসার কথা। কিন্তু তারা তো এখনও এসে পৌঁছায়নি।
–কিন্ত রোম-সার্ভিস তো ঠিক সময়েই এসেছে। সে তো ঘণ্টাচারেক হল।
তবে বোধহয় কোনো হোটেলে উঠেছে। আপনার নামটা বলুন। ও এলে বলব।
-কিছু মনে করবেন না। তাকে একটা সারপ্রাইজ দিতে চাই। সে এলে দয়া করে ওকে বলবেন না আমি ফোন করেছিলাম।
-ও আচ্ছা, আচ্ছা। তবু আপনার নাম্বারটা বলুন। ও এলে আপনাকে রিং করব।
–আমি একটা পাবলিক বুথ থেকে ফোন করছি। আমি কাল সকালে নিজেই ফোন করব বরং। শুভরাত্রি
কিন্তু রাত্রিটা বোধহয় ‘শুভ’ নয়। ও তৎক্ষণাৎ বের হয়ে পড়ল হোটেল থেকে। ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেল এয়ারপোর্টে। সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন ধোঁয়াটে লাগছে। ওখানকার সিকিউরিটি অফিসারকে আত্মপরিচয় দিল। তার সাহায্য চাইল। আন্তর্জাতিক সৌজন্যের খাতিরে সিকিউরিটি অফিসার ওকে সাহায্য করতে রাজি হলেন। রাত সাতটার পর যে সব যাত্রীবাহী প্লেন বিমানবন্দর ত্যাগ করেছে তার তালিকাটি দেখাই হল প্রথম কাজ। বেশি খুঁজতে হল না। দেখা গেল রাত নটার একটা প্লেনে ডক্টর ব্রুনো স্বনামে টিকিট কেটে সপরিবারে হেলসিঙ্কি চলে গেছেন। ফিনল্যান্ড যাবার পাসপোর্ট ছিল তার।
সর্বনাশ! পরবর্তী প্লেনে স্কার্ডন চলে গেল হেলসিঙ্কি। বৃথাই। সেখানে সংবাদ পাওয়া গেল, পূর্ববর্তী প্লেনে ডক্টর ব্রুনো সপরিবারে এসেছিলেন। কিন্তু তিনি তারপর কোথায় গেলেন কেউ জানে না।
অনেক পরে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড অনুমান করেছে–হয় এখান থেকে রাশিয়ান এম্বাসির সহযোগিতায় ডিপ্লোম্যাটিক পাসপোর্টে ব্রুনো ছদ্মবেশে রাশিয়ায় চলে যান। অথবা মোটরে করে তাদের সঙ্গে সীমান্ত পার হয়ে যান। মোট কথা, ব্রুনোর খবর আর পাওয়া যায়নি।
অ্যালান নান মে ধরা পড়ল। আর ব্রুনো পন্টিকার্ভো–এ কাহিনির দু-নম্বর গুপ্তচর ডাস-হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।
সাত বছর পরে প্রাভদায় প্রাকশিত একটি প্রবন্ধে ব্রুনোর অন্তর্ধান-রহস্যে শেষ যবনিকাপাত ঘটল। জানা গেল, ব্রুনো বহাল তবিয়তে মস্কোতে একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাকার্যে নিযুক্ত আছেন। হেলেনার সঙ্গে তার বাপ-মায়ের আর কোনোদিন সাক্ষাৎ হয়নি।
নিঃসন্দেহে ব্রুনো বুঝতে পেরেছিল তাকে সন্দেহ করছে এফ. বি. আই. এবং স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড। লিভারপুলে চাকরি নেওয়া, শ্যামনীতে কনফারেন্সে যাবার প্রতিশ্রুতি, রোমে রিটার্ন-টিকিট কাটা, স্টকহমের হোটেলে দুখানি ঘর ভাড়া করা সবই তার দীর্ঘমেয়াদি পলায়নপ্রকল্পের প্রস্তুতি। নিঃসন্দেহে সে মিলানের আমেরিকান টুরিস্ট এবং রোমের ফরাসি আর্টিস্টটিকে চিহ্নিত করেছিল। আর সেই জন্যেই সে স্টকহম এয়ারপোর্টে স্ত্রীকে উচ্চকণ্ঠে জানিয়েছিল তার হোটেলের নাম। স্কটল্যান্ড-ইয়ার্ডের পাকা গোয়েন্দার নাকে ঝামা ঘষে দিয়ে যেভাবে সে পালালো সেটা গোয়েন্দা গল্পেই সম্ভব–যদিও এটা আদ্যন্ত বাস্তব ইতিহাস।
ব্রুনো বোধকরি আর একটা প্রমাণ রেখে গেল ফাইনম্যানের সেই ঋষিবাক্যটির :E = mc^2 অপরাধ-বিজ্ঞানী কোনোদিনই বুঝবে না; কিন্তু ধূর্ততার প্রতিযোগিতায় নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্টের কাছে পাকা-গোয়েন্দাও-ফুস।
‘অ্যালেক’ শেষ হয়েছে, ‘ডগলাস’ শেষ হল–এবার বাকি রইল পালের গোদা : ডেক্সটার। তার কথাই বলি :
৭. কেন ৫-৮
০৫.
ফাইনম্যানকে কিন্তু ধরাছোঁয়ার মধ্যে পাওয়া গেল না। ম্যাককিলভি দীর্ঘদিন লেগে ছিল তার পিছনে, ছায়ার মতো। কোনো নূতন সূত্র আবিষ্কার করতে পারেনি। অবশেষে কর্নেল প্যাশ নিজেই একদিন এসে হাজির হল প্রফেসর ফাইনম্যানের ডেরায়। সমাদর করে ফাইনম্যান তাকে বসালোলা নিজের বৈঠকখানায়। আবহাওয়া থেকে শুরু করে সিনেমা, বেল সব কিছু আলোচনা করল খোশমেজাজে, কফি খাওয়ালো। শেষমেশ লস অ্যালামসের প্রসঙ্গ তুলতে বাধ্য হল প্যাশ। ফাইনম্যান তৎক্ষণাৎ বললে, আপনার আইডেন্টিটি কার্ডটা দেখাবেন দয়া করে?
কর্নেল প্যাশ তৈরি হয়েই গিয়েছিল। তৎক্ষণাৎ তার সনক্তিকরণ কাগজপত্র দেখালো অধ্যাপককে–সে সিকিউরিটির লোক, লস অ্যালামস সম্বন্ধে আলোচনা করার অধিকার তার আছে এটা প্রমাণ করল। বললে, এবার আপনাকে আমি কিছু ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে চাই; কিছু মনে করবেন না–
করলেই বা ঠেকাচ্ছে কে? স্বচ্ছন্দে প্রশ্ন করে যান।
–পিটার নামে আপনার কোনো পুত্রসন্তান ছিল, বা আছে?
আজ্ঞে না। আমার আদৌ কোনো পুত্রসন্তান হয়নি। ছিল না, বা নেই।
–মিসেস ওবমোতা নামে একটি গভর্সেকে আপনার পুত্রের জন্য কখনও নিয়োগ করেছিলেন একগাল হাসল ফাইনম্যান। বললে, আপনার প্রশ্নটাই অবৈধ। হয়ে পড়ছে নাকি, অফিসার? আমার পুত্রই নেই, তার জন্য গভর্নের্স?
-আই মিন, ওই নামে কাউকে আপনি চেনেন?
–না, চিনি না।
–অথচ লস অ্যালামসে থাকতে একটি চিঠিতে আপনি পিটার এবং মিসেস ওবমোতার উল্লেখ করেছিলেন?
-না।
–না? আমার কিন্তু একজন সাক্ষী আছে।
আনন্দের কথা। সাক্ষীকে কাঠগড়ায় যখন তুলবেন তখন তাকে আমি ক্রস্-এগজামিন করব। জিজ্ঞাসা করব পিটার বানান কী? ওই বানানে সে আমার লেখা কোনো চিঠিতে
–একজ্যাক্টলি। ওই বানানে লেখেননি। উল্টো করে লিখেছিলেন–
-কর্নেল! আপনি গোয়েন্দা আমি বিজ্ঞানী–কিন্তু আমরা আলোচনা করছি ইংরেজি ভাষা নিয়ে। কোনো ভাষাবিদকে ডাকলে হয় না? আর-ই-টি-ই-পি বানানে পিটার উচ্চারণ শাস্ত্রসম্মত কিনা
এবারও বাধা দিয়ে প্যাশ বলে, দেখুন প্রফেসর, আপনি ক্রমাগত ব্যাপারটাকে এড়িয়ে যাচ্ছেন। এটা আদৌ কোনো রসিকতার কথা নয়। আপনি কি নিজেই আমাদের সিকিউরিটি অফিসারকে বলেননি অক্ষরগুলো উল্টোপাল্টা করে লিখেছেন?
-বলেছিলাম। না হলে সে আমার চিঠি পাস্ করছিল না।
–অথচ অক্ষরগুলো মোটেই উল্টোপাল্টা করে সাজানো নয়, স্রেফ উল্টো করে সাজানো–কেমন?
-তাই নাকি?
–এবং পিটার একজন রাশিয়ান এজেন্ট।
–বলেন কী!
–অথচ আপনি ম্যাককিলভিকে বলেছিলেন, পিটার আপনার ছেলের নাম, মিসেস ওবমোতা আপনার গভর্নেসের নাম?
-বলেছিলাম।
–কেন?
–ওই তো বললাম-না হলে সে আমার চিঠি পাস্ করত না।
–তাহলে আসলে আপনি আপনার স্ত্রীকে কী কথা জানিয়ে ছিলেন? ফাইনম্যান সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে, লুক হিয়ার অফিসার, আমার স্ত্রীকে আমি চিঠিতে কী লিখেছি তা জানাতে আমি বাধ্য নই। আমি বলব না।
–আমার কাছে অস্বীকার করতে পারেন। কিন্তু কোনো এনকোয়ারি কমিশনের কাছে—
ফাইনম্যান হেসে বলে, আপনি ভুল করছেন অফিসার। ওভাবে হবে না। এনকোয়্যারি কমিশন পর্যন্ত যেতেই পারবেন না আপনারা। ওই চিঠিখানির অস্তিত্বই প্রমাণ করতে পারবেন না। তাছাড়া আমার অ্যাডভোকেট আপনাদের তো ছেড়ে কথা বলবে না। আমি তো অমন চিঠির কথা মনেই করতে পারব না। আপনাদেরই বরং জবাবদিহি করতে হবে, কেন অমন চিঠি আপনারা পাস’ করলেন–আদৌ যদি চিঠির অস্তিত্বটা মেনে নেওয়া হয়।
কর্নেল প্যাশ এবার তার আক্রমণ-পদ্ধতি পরিবর্তন করতে বাধ্য হল। সত্য। কথা–ওই চিঠিখানার অস্তিত্ব প্রমাণ করা শক্ত। সেটা স্বীকার করা মানে, প্রমাণ করা লস অ্যালামসে সিকিউরিটিম্যান অপদার্থ ছিল। প্যাশ এবার প্রশ্ন করে, এ কথা কি সত্য যে, আপনি কম্বিনেশান-চাবির সাহায্যে কারচুপি করে লস অ্যালামসের ‘আয়রন-সেফ’ একদিন খুলে ফেলেছিলেন?
ফাইনম্যান বলে, তা কেমন করে সম্ভব? সেখানে তো সর্বক্ষণ প্রহরা থাকত।
–আমি নিশ্চিন্তভাবে খবর পেয়েছি–প্রহরী মিনিট পনেরোর জন্য অনুপস্থিত ছিল, আর তখন আপনি সেফটি খোলেন।
ফাইনম্যান অট্টহাস্য করে ওঠে। বলে, কী বকছেন মশাই পাগলের মতো? আপনি কি এই আষাঢ়ে গল্পও এনকোয়্যারি-কমিশনকে শোনাতে চান নাকি?
–আপনি সোজাসুজি আমার প্রশ্নের জবাব দিন। এ অভিযোগ আপনি অস্বীকার করছেন? ‘হ্যাঁ’ না ‘না’?
ফাইনম্যান গম্ভীর হয়ে বললে, এককথায় ওর জবাব হয় না। আমাকে কতকগুলি প্রতিপ্রশ্ন করতে দিতে হবে–
-বলুন?
–ওই আয়রন-সেফ-এ মার্কিন-যুক্তরাষ্ট্রের গোপনতম তথ্য রাখা হত–এ কথা সত্য?
-ইয়েস।
–তাই ওই সেফটি বসানোর আগে তার নিরাপত্তা বিষয়ে এফ. বি. আই.-কে দিয়ে পরীক্ষা করানো হয়েছিল–আপনারা লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন সেটা কেউ খুলতে পারবে না।’হ্যাঁ’ না ‘না’?
কর্নেল প্যাশ ইতস্তত করে বলে : ইয়েস।
অথচ এখন আপনি বলছেন, পনেরো মিনিটের মধ্যে একজন ফুস-মন্তরে সেটা খুলে ফেলল। কেমন? তার অনুসিদ্ধান্ত কী? আপনারা অপদার্থ না গল্পটা আষাঢ়ে?
কর্নেল প্যাশ চটে উঠে বললে, জেরা কে করছে? আপনি না আমি?
–আপনার অনুমত্যনুসারে আপাতত আমি।
-না। আমি প্রশ্ন করব, আপনি জবাব দেবেন। বলুন–কোর্টে দাঁড়িয়ে হলপ নিয়ে আপনি এ অভিযোগ অস্বীকার করতে পারেন?
আগে কোর্টে তুলুন মশাই। আদালতের কথা আদালতে হবে। আপাতত এটা আমার ড্রইংরুম।
কর্নেল প্যাশ উঠে দাঁড়ায়। দ্বারের দিকে পা বাড়ায়।
–জাস্ট এ মিনিট কর্নেল-পিছন থেকে ফাইনম্যান ডাকে।
–ইয়েস?
–আপনার সেই মাথামোটা বন্ধু ম্যাককিলভিকে বলবেন–আমার চিঠিখানা পুড়িয়ে ফেলে সে বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেনি। একটু তদন্ত করলে সে জানতে পারত চিঠিখানা আমার ব্যক্তিগত টাইপরাইটারে টাইপ করা–
–কোন্ চিঠিখানা?
–আপনি জানেন না। সে জানে। যেখানায় তাকে আমি চারটে জরুরি খবর জানিয়েছিলাম। রাখলে, সেখানাই আমার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় এভিডেন্স হতে পারত। তাকে জিজ্ঞাসা করবেন। সব কথা এবার সে স্বীকার করবে।
***
রবার্ট জে. ওপেনহাইমারও আমাদের কাহিনির কেন্দ্রবিন্দু থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছেন। আমরা ভুললেও এফ. বি. আই. তাকে ভোলেনি। ইতিমধ্যে গোয়েন্দা হাত বদলেছে। কর্নেল প্যাশ তার নথিপত্র বুঝিয়ে দিয়েছেন তার উত্তরসূরী এডগার হুভারকে। এফ. বি. আই. ওপেনহাইমারের ব্যাপারে সর্বক্ষণের জন্য একটি স্পেশাল গোয়েন্দা লাগালেন। নবনিযুক্ত এই গোয়েন্দাটি ছায়ার মতো অনুসরণ করে চলেছে ওপিকে।
যুদ্ধজয়ের অব্যবহিত পরেই ওপেনহাইমার লস অ্যালামাসের ডিরেকটারের আসন থেকে পদত্যাগ করলেন। অনেকেই বিস্মিত হল এ সিদ্ধান্তে। ওপি সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের বললেন–অতঃপর বৈজ্ঞানিক গবেষণাই তার জীবনের ব্রত। মারণাস্ত্র নয়, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে নিযুক্ত হতে চান তিনি। প্রকৃত বিজ্ঞানভিক্ষুর মতো কথা।
ইতিমধ্যে কিন্তু আমূল পরিবর্তন হয়েছে তার জীবনদর্শনে। খ্যাতির মোহ পেয়ে বসেছে তাঁকে। একের পর একটি সম্মান পেয়ে যাচ্ছেন তিনি। কাগজে কাগজে ফলাও করে বার হচ্ছে তার নাম। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান যুদ্ধান্তে তাকে সে বছরই দিলেন- ‘মেডেল অফ মেরিট’। ন্যাশনাল বেবি ইনস্টিটুট তাকে সে বছর ‘ফাদার অফ দ্য ইয়ার’ বলে ঘোষণা করল। ‘পপুলার মেকানিস্ট’ নামে একটি পত্রিকা এক বিশেষ সংখ্যায় তাকে খেতাব দিল ‘বিংশশতকের প্রথমার্ধের শ্রেষ্ঠ মনীষী’। আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, গান্ধীজী, রোমাঁ রোঁলা, ফ্রয়েড, বার্নাড শ-কে পিছনে ফেলে ওপি ‘সবিনয়ে’ গ্রহণ করলেন এ খেতাব। অনেক কাগজেই তাকে উল্লেখ করা হচ্ছে ‘অ্যাটম-বোমার জনক’ হিসাবে। সহস্রাধিক বৈজ্ঞানিকের প্রাপ্য সম্মানটাও নির্বিচারে গ্রহণ করলেন ওপি। তিনি তার প্রাইজ, খেতাব, এবং মানপত্রগুলি রোজই নাড়াচাড়া করেন। সস্ত্রীক ইউরোপ ভ্রমণে গেলেন। একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কুড়িয়ে আনলেন ‘অনারারি ডক্টরেট’। সংবাদপত্রে তাঁর নামে যেখানে যা কিছু ছাপা হয় তা সাজিয়ে রাখেন ফাইলে। এ কাজের জন্য শেষ পর্যন্ত একটি সেক্রেটারি পর্যন্ত নিযুক্ত করলেন ওপি।
লোভ থেকে মোহ–তা থেকে অহঙ্কার। আমূল বদলে গেলেন ওপেনহাইমার। দিবারাত্র বক্তৃতা দিয়ে বেড়ানোই হল তার কাজ। আজ এখানে দ্বারোঘাটন, কাল সেখানে সভাপতিত্ব, পরশু ওখানে প্রধান-অতিথি। ক্লাস নেওয়াও হয়ে ওঠে না সবসময়ে। 1943 থেকে 53–এ দশ বছরের মধ্যে তিনি মাত্র পাঁচটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখার সময় করে উঠতে পেরেছিলেন এবং বিশেষজ্ঞদের মতে সেগুলিও নেহাৎ মামুলি। অথচ বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আইনস্টাইনের মতো লোককেও তিনি কড়া সমালোচনা করতে কসুর করেননি। ওঁর একজন দীর্ঘদিনের বন্ধু এই সময়ে লিখেছেন, “যেদিন ওপি জেনারেল মার্শালকে শুধু ‘জর্জি’ বলে উল্লেখ করল সেদিনই বুঝলাম আমরা ভিন্ন পথের পথিক হয়ে গিয়েছি। মনে হয় আকস্মিক খ্যাতিতে ওর মাথা ঘুরে গিয়েছিল।…সে নিজেকে মনে করত সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের অবতার। যেন দুনিয়াটাকে ঠিক পথে চালিত করার দায়িত্ব শুধু ওর স্কন্ধের ওপর আরোপিত!”
ওপি নিজেকে যাই ভাবুক না কেন গোয়েন্দা হুভার তাকে বিশ্বাসঘাতক ছাড়া আর কিছু ভাবত না। নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবুনের বিশেষ সংবাদদাতা লিখেছেন, 1953 সালের নভেম্বর-তক ওপেনহাইমার-সংক্রান্ত নথিপত্র এত জমেছিল যে, ফাইলগুলি একের পর এক সাজানো হলে তা সাড়ে চার ফুট উঁচু হয়ে যেত। অর্থাৎ মানুষটার বিরুদ্ধে প্রমাণ প্রায় মানুষ-প্রমাণ! হুভার ওই মাসেই সেই। পর্বতাকৃতি নথিপত্র ঘেঁটে একটা সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট তৈরি করল। ম্যানহাটান প্রকল্পের বিভিন্ন নথিপত্র থেকে ওপি যেমন সঙ্গোপনে একটি মাত্র বোমা তৈরি করতে বসেছিলেন, ঠিক সেই ভঙ্গিতেই হুভার তৈরি করল আর একটি পরমাণু বোমা। ওপেনহাইমার তার বিন্দুবিসর্গও জানেন না। যুদ্ধকালে হিরোশিমার জিয়ানো কইমাছগুলোও বোধকরি এত নিশ্চিন্ত ছিল না। ইন্ডিয়ানাপোলিস জাহাজে যেমন অতি সঙ্গোপনে পাচার করা হয়েছিল প্রথম বোমাটা–ঠিক তেমনি করেই হুভার তার রিপোর্টখানা সন্তর্পণে পাঠিয়ে দিলেন সর্বোচ্চ দপ্তরে; এমনকি একটি কপি খাস আইসেনহাওয়ারের কাছে। না জেনারেল আইসেনহাওয়ার নয়, প্রেসিডেন্ট আইক-এর দপ্তরে। এতদিনে ট্রুম্যানের চেয়ারে এসে বসেছেন আইক।
তাতে কাজ হল।
রিপোর্টে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সাজিয়েছেন হুভার। যুক্তিনির্ভর তথ্য :
প্রথমত, ওপেনহাইমার দীর্ঘদিন ধরে কম্যুনিস্টদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাদের অনেক রুদ্ধদ্বার কক্ষের মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন। অনেক কম্যুনিস্ট ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল তাঁর। ওপির স্ত্রী, ভাই ও ভ্রাতৃবধূ কম্যুনিস্ট। ওপেনহাইমার ছদ্মনামে ওদের মুখপত্রে প্রবন্ধ লিখেছেন, পার্টি ফান্ডে চাঁদা দিয়েছেন। তার অকাট্য প্রমাণ আছে।
দ্বিতীয়ত, 1943-এর সেই বারোই জুন ওপি যে মেয়েটির সঙ্গে রাত কাটান সেই মিস ট্যাটলক একজন নামকরা কম্যুনিস্ট এজেন্ট। ওই সাক্ষাৎকারের পর মেয়েটি আত্মহত্যা করে। কারণটা অজ্ঞাত।
তৃতীয়ত, ওপেনহাইমার সজ্ঞানে মিথ্যাভাষণ করেছেন-হাকন শেভেলিয়ার আদৌ গুপ্তচরবৃত্তি নেননি। দীর্ঘদিন ওই শেভেলিয়ারের পেছনে এফ. বি. আই. গুপ্তচর নিযুক্ত করে নিঃসন্দেহে বুঝেছে তিনি জীবনে কখনও রাশিয়ান গুপ্তচরদের সংস্পর্শে আসেননি। ওপেনহাইমার তার মিথ্যাভাষণে একজন নিরীহ পণ্ডিতের সর্বনাশ করেছেন।
প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার সচরাচর এসব ব্যাপারে নাক গলাতেন না। অধীনস্থ কর্মচারীদের যথাকৰ্তব্য করতে দিতেন। এক্ষেত্রে কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটল। তিনি তৎক্ষণাৎ কয়েকজন অতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীকে হোয়াইট হাউসে ডেকে পাঠালেন। সংক্ষিপ্ত অধিবেশন। মিলিটারিম্যান আইসেনহাওয়ার তার কোনো কর্মচারিকে ‘দিস রিকোয়ার্স এ্যাকশান’ বলেছিলেন কিনা জানি না–কিন্তু ব্যবস্থা হল অবিলম্বে।
ওপেনহাইমার তখন প্রিন্সটাউনে। আসন্ন বড়দিনের উৎসবে ব্যস্ত। হঠাৎ একটা জরুরি টেলিগ্রাম এল ওয়াশিংটন থেকে–অ্যাটমিক-এনার্জি কমিশনের চেয়ারম্যান তাকে অবিলম্বে দেখা করতে বলেছেন। একুশে ডিসেম্বর সব কাজ ফেলে ওপি ছুটে এলেন ওয়াশিংটনে। দেখা করলেন চেয়ারম্যানের সঙ্গে। তখনই তার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হল চার্জশিট। দীর্ঘ অভিযোগের তালিকা। বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত।
বজ্রাহত হয়ে গেলেন ‘বিংশশতাব্দীর প্রথমার্ধের শ্রেষ্ঠ প্রতিভা।
যোজনবিস্তৃত সর্ষে ফুলের ক্ষেত নয়; তিনি দেখলেন–’প্রকাণ্ড একটা ধোঁয়ার বলয় পাক খেতে খেতে ওপরে উঠে যাচ্ছে–একটা আগুনের বলয়, তার কিনারাগুলো সিদুরে লাল…অনাবিষ্কৃত একটা নগ্নসত্য উদঘাটিত হল চোখের সামনে…ঘনিয়ে এল মহামৃত্যু।
অস্বাভাবিক একটা নীরবতা। পুরো দেড় মিনিট ওপেনহাইমার কথা বলেননি।
শুরু হল ওপেহাইমারের ঐতিহাসিক বিচার। বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে।
সেটা কিন্তু 1954-র এপ্রিল মাসে। বস্তুত বিশ্বাসঘাতক ‘ডেক্সটার’ ধরা পড়ার চার বছর পরে। আমাদের মূল কাহিনির এক্তিয়ারের বাইরে।
আজ্ঞে না। ওপেনহাইমার ‘ডেক্সটার’ নন।
.
০৬.
ক্লাউস ফুকস্ আর সস্ত্রীক প্রফেসর কার্ল গ্রীশ্মাবকাশ কাটাতে এলেন পারিতে।
হঠাৎই এ সিদ্ধান্ত। প্রস্তাবটা প্রথমে তুলেছিলেন প্রফেসর কার্ল অন্যভাবে। কী একটা প্রয়োজনে তাকে দিন তিন-চারের জন্য পারিতে যেতে হবে। কারণটা কী তা উনি খুলে বলেননি। তখন রোনাটা হঠাৎ বলে বসে, তাহলে আমরাও কেন যাই না সঙ্গে? ক্লাউস-এর নতুন গাড়িটার একটা পরখ হয়ে যাবে। কী বল ক্লাউস?
ক্লাউস তার পুরনো গাড়িটা বেচে সম্প্রতি একটা ভালো সিডানবডি গাড়ি কিনেছে। সেটা নিয়ে পারি ভ্রমণে যেতে তার আদৌ আপত্তি নেই, আগ্রহ আছে। সেসব কথা নয়, ও ভাবছিল হঠাৎ রোনাটার এ মত পরিবর্তনের কারণটা কী? ইতিপূর্বে সে তো একদিন অন্তিম ফতোয়া জারী করে বসে আছে ক্লাউস তাদের বাড়িতে একেবারে না এলেই ভালো হয়।
মোটকথা ব্যবস্থা হল। সব কিছু আয়োজন করলেন প্রফেসর কার্ল। পারিতে হোটেলের ঘর বুক করলেন তিনিই। তারপর একদিন ওঁরা রওনা হয়ে পড়লেন। গাড়ি নিয়ে। লন্ডন থেকে পারি।
ওঁরা এসে উঠলেন পিগেল অঞ্চলে হোটেল ইন্টারন্যাশনালে। প্রকাণ্ড হোটেল। ব্যবস্থাপনা ভালো। প্রফেসর আগেভাগেই দু-খানি ঘর ‘বুক’ করেছেন। সাততলায়। রুম নম্বর 728 এবং 729। দুটোই দ্বৈতশয্যার। ক্লাউস-এর পক্ষে এতবড় কামরার প্রয়োজন ছিল না কিন্তু পাশাপাশি থাকা যাবে এই মনে করে প্রফেসর ওই ব্যবস্থা করেছিলেন। 729-এ উঠলেন সস্ত্রীক কার্ল এবং 728-এ একা ফুকস।
পারিতে পৌঁছেই কিন্তু অতি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন প্রফেসর কার্ল। দিনপঞ্জিকায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট তার ঠাসা। বেড়ানোর সময় নেই আদৌ। রোনাটা অভিযোগ করলে বলেন, আমি তো আগেই বলেছিলাম–আমি বেড়াতে আসছি না, কাজে আসছি। তা তোমার অসুবিধা কী আছে? ঘোর না যত খুশি। ক্লাউস তো আছে সঙ্গ দিতে।
অগত্যা ক্লাউসকেই ঘুরতে হচ্ছে। লুভর মিউজিয়াম, আর্ক-দ্য-ত্রিয়ম্ফ, ঈফেল-টাওয়ার, নতরদাম গির্জা। ভালোই লাগছিল ফুকসের। দুজনের মধ্যে কোনো চুক্তি হয়নি, কিন্তু সেই প্রসঙ্গটা কেউই আর উত্থাপন করেনি। বন্ধুত্বের সম্পর্কেই আনন্দ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সন্ধ্যায় নৌকাযোগে সেইন-এ বেড়াচ্ছে। রাস্তার ধারে খোলা রেস্তোরাঁয় আহারাদি সেরে হোটেলে ফিরছে রাত করে।
পুরানো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায় ক্লাউস-এর। তার যৌবনের দিনগুলোর কথা। সেই যখন সে ছিল রোনাটার বাবার আশ্রয়ে। তখনও এমনিভাবে ওরা দুজন বেড়াতে যেত। ও ছাড়া আর কারও সঙ্গে ডেটিং’করত না। রোনাটা। তাহলেও মেয়েটা ছিল অত্যন্ত সাবধানী, রক্ষণশীল। বেশি দূর অগ্রসর হতে দেয়নি কখনও তাকে। একসঙ্গে সিনেমা দেখেছে, থিয়েটার দেখেছে, নেচেছে, গল্প করেছে। ব্যস, তারপর অগ্রসর হতে চাইলেই সরে গেছে রোনাটা। অথচ ক্লাউস-এর বেশ মনে আছে, রোনাটা সে-যুগে তাকে ঘিরে ময়ূরের মতো পেখম মেলে নাচত। জীববিজ্ঞানের নিরিখে তুলনাটা হয়তো ঠিক হল না, কিন্তু বাস্তবে ঘটনাটা ওইরকমই হত। সে-আমলে রোনাটার প্রসাধন, সাজসজ্জা, অঙ্গভঙ্গি, বাকচাতুর্য সবকিছুই ছিল ওই তরুণ ছাত্রটির মনোহরণের উদ্দেশ্যে।
একদিনের ঘটনা ওর বিশেষ করে মনে পড়ে। সেই একটি দিনই ও উদ্দাম হয়ে উঠেছিল। তখনও রোনাটার বাবা বেঁচে। সে রাত্রে লন্ডনে বিখ্যাত ওল্ড ভিক’ গ্রুপের রোমিও-জুলিয়েট হচ্ছে। ক্লাউস দুখানা টিকিট কেটে এনেছিল। রোনাটা একমাত্র তার সঙ্গে তখন ‘ডেটিং’ করছে–ওর বাবা জানেন সে কথা। অনুষ্ঠান দেখে যখন ফিরে এল তখন শহরতলীতে নিশুতি রাত। বাড়ির সবাই শুয়ে পড়েছে। দ্বিতল বাড়ি। একতলায় ক্লাউস-এর শোওয়ার ঘর–ভাইবোনদের নিয়ে রোনাটা থাকত দ্বিতলে। সদর দরজার ডুপ্লিকেট চাবি থাকত ওদের কাছে। আহারাদি সেরে এসেছিল ওরা। ওকে শুভরাত্রি জানিয়ে রোনাটা যখন দ্বিতলে উঠে যাচ্ছে তখন হঠাৎ গ্লাভস-সমেত হাতটা চেপে ধরেছিল ফুকস্। রোনাটা প্রথমটা বুঝতে পারেনি। বলেছিল, কী?
ফুকস-এর রক্তে তখন তুফান জেগেছে। কোনো কথা বলেনি সে। জোর করে ওকে টেনে নিয়েছিল নিজের বুকে। প্রথমটা বিস্ময়, তারপরেই শিউরে উঠেছিল রোনাটা। দু-হাতে ওকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল–বাধা দিয়েছিল। ফুকস্ সে বাধা মানেনি। জোর করে চেপে ধরেছিল ওর পায়রার মতো নরম বুক নিজের পেশীবহুল কবাট বক্ষে। কী যেন বলতে চেয়েছিল রোনাটা–পারেনি। ফুকসের উন্মুক্ত ওষ্ঠাধরে সে প্রতিবাদের ভাষাটা হারিয়ে গিয়েছিল। অদ্ভুত একটা অনুভূতি। আজও ভোলেনি সে কথা। কখন অজান্তে রোনাটার প্রতিবাদ-উদ্যত বাহুজোড়া ওকে সবলে আলিঙ্গন করে ধরেছিল। সেই ওকে প্রথম চুম্বন করে। এবং সেই শেষ। এর চেয়ে আর একটি পদও তাকে অগ্রসর হতে দেয়নি মেয়েটি।
পরে এ নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। ক্লাউস বলেছিল–ইচ্ছের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই নয়, তাহলে তুমি আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলে কেন? রোনাটা দু-হাতে মুখ ঢেকে বলত–প্লিজ, ক্লাউস, ও-প্রসঙ্গ তুললে আমি তোমার সামনে আর আসব না। আশ্চর্য লাজুক মেয়েটা। না, লাজুক নয়–রক্ষণশীল। ও কিন্তু মধ্যযুগের মেয়ে নয়, চার্চের ‘নান’ নয়, কলেজে-পড়া আধুনিকা। তার সহপাঠিনীরা ‘ডেটিং’ করতে গিয়ে সপ্তপদীর কয় পা অগ্রসর হত, সে কথা নিশ্চয় জানা ছিল তার। কিন্তু ধর্মের এক ভূত চেপে বসেছিল রোনাটার ঘাড়ে। কুমারী মেয়ের কৌমার্য সম্বন্ধে সে ছিল অস্বাভাবিক রকমের সচেতন–আর সে কৌমার্য ওর ঠোঁটে, বুকে, সর্বাঙ্গে। আশ্চর্য মেয়ে!
তবু তার একটা অর্থ হয়। প্রাকবিবাহযুগে কুমারী মেয়ের সহজাত সংস্কার। কিন্তু এর অর্থ কী? আজ কেন সেই পরিণতবয়স্কা মেয়েটি হঠাৎ বলে বসল : বিবাহের সংজ্ঞা ইন্দ্রিয়জ ব্যভিচারের একটা পাসপোর্ট নয়?
***
প্রফেসর কার্ল গোটা-তিনেক ক্যামেরা এনেছেন–কিন্তু ফটো তোলার মত সময় অথবা মেজাজ নেই তার। অগত্যা রোনাটা আর ক্লাউস আনাড়ি হাতে তার সদ্ব্যবহার করে। এখানে-ওখানে ফটো তুলে বেড়ায়। সেদিন ওরা গেল শহরের বাইরে ভার্সাইপ্রাসাদ দেখতে। লুই পরিবারে বিলাস-ব্যসনের স্মৃতি-বিজড়িত ভার্সাই প্রাসাদ। অনেক ফটো নিল। তারপর প্রাসাদের পিছন দিকের সুন্দর বাগানটিতে গিয়ে বসল ওরা। টুরিস্ট অনেক এসেছে, বাগানটাও অতি প্রকাণ্ড। দূরতম প্রান্তে একটা কারনেশান-বেড এর ধারে ওরা যেখানে গিয়ে খাবারের বাস্কেট খুলল, সেখানটা প্রায় নির্জন। ফুকস্ তার ফ্লাস্ক বার করে দু-পাত্র ব্র্যান্ডি ঢালল। রোনাটা বললে, আজ আমরা এই যে বাগানটায় নির্জনে বসে লাঞ্চ খাচ্ছি, এখানেই একদিন হয়েছিল ‘টেনিস কোর্ট বিদ্রোহ’ তা জান?
–টেনিস-কোর্ট বিদ্রোহটা কী?
-তুমি কি নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ছাড়া আর কিছু পড়নি? ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস?
-না। অত সময় আমার নেই।
–তবে ও প্রসঙ্গ থাক। গোটা ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাস শোনাবার মতো মেজাজ আমার নেই।
–তবে থাক।
দুজনে কিছুক্ষণ নীরবে পানাহার করতে থাকে। তারপর ফুকস্ বলে, আচ্ছা সত্যি করে বলত রোনাটা–তুমি কী চাও? আমি ইস্ট-জার্মানিতে চাকরি নিয়ে চলে গেলে তুমি খুশি হও, না বকে নিয়ে এসে এখানেই যদি রাখি?
রোনাটা মিষ্টি হাসে। বলে, কী মনে হয়?
–কী জানি, ঠিক বুঝতে পারি না। এক-এক সময় মনে হয় আমি তোমার চোখের আড়ালে চলে গেলেই শান্তি পাবে তুমি।
–নিজের গুরুত্বটা বড় বেশি করে দেখছ না?
–তুমিই তো বললে সেদিন।
-সে তো রাগের মাথায়।
–তবে মনের কথাটা কী?
–এতদিনেও যদি না বুঝে থাক, তবে বুঝে আর কাজ নেই।
-কিন্তু স্পষ্ট করে না বললে কেমন করে আমি সিদ্ধান্ত নেব। ও চাকরি নেব কি না?
ম্লান হাসল রোনাটা। বললে, আমার ইচ্ছার সঙ্গে তোমার সিদ্ধান্ত নেবার কী সম্পর্ক? আমাকে খুশি করতেই কি সারাজীবন ধরে সিদ্ধান্ত নিয়েছ তুমি?
-না, তা নিইনি। তোমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলাম একদিন…
–সে কথা কিন্তু আমি ‘মিন’ করিনি। ও কথা বরং থাক।
–তবে কী কথা আলোচনা করব? আজকের আবহাওয়া?
–না। অন্য কিছু।
–তবে তোমার কথা বল।
–কী আমার কথা?
–তুমি আবার ‘মা’ হচ্ছ না কেন?
–আবার ‘মা’। মানে?
–অ্যালিসের কোনো ছোটো ভাই অথবা বোন?
ম্লান হাসল রোনাটা। যক্ষ্মারোগীর রক্তশূন্য পাণ্ডুর হাসি। ব্র্যান্ডিটা গলায় ঢেলে দিয়ে বললে, ফর য়োর ইনফরমেশন জুলি, অ্যালিস আমার মেয়ে নয়।
দ্বিতীয় পানপাত্রটা তুলেছিল ক্লাউস। ধীরে ধীরে এবার তার হাতটা নেমে আসে। অবাক হয়ে বলে, মানে? অ্যালিস তোমার মেয়ে নয়?
–না। অ্যালিস প্রফেসর কার্ল-এর প্রথম পক্ষের কন্যা।
ক্লাউস-এর মনে পড়ে গেল অ্যালিসের চেহারা। অ্যালিস ছিল ব্রুনেট– মাথাভরা কালো চুল। অথচ রোনাটা ব্লন্ডি। তাই মেয়ে মায়ের মতো দেখতে হয়নি আদৌ। অস্ফুটে বললে, আশ্চর্য। এত বড় খবরটা এতদিন আমাকে বলনি তো?
-শুধু তাই নয় জুলি। অ্যালিস প্রফেসর অটো কার্লের মেয়েও নয়।
তার মানে?
–অ্যালিসের মাকে তিনি বিবাহ করেন ওই কন্যা সমেত।
হঠাৎ ক্লাউস ওর গ্লাভস-পরা হাতটা চেপে ধরে–যেভাবে একদিন তার হাত চেপে ধরেছিল প্রথম যৌবনে, সিঁড়ির মুখে। বলে, ডাক্তার দেখিয়েছিলে? অসুস্থ কে? তুমি, না প্রফেসর?
–অসুস্থ হতে হবে তার মানে কী?
রোনাটা তার হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। বলে, পাগলামি কোরো না। এখানে আরও লোক আছে।
ক্লাউস তার হাতটা ছেড়ে দেয়। রোনাটা ঘড়ি দেখে বলে–সময় হয়ে গেছে। চল, ওঠা যাক। বাসটা ছেড়ে দেবে না হলে।
ওরা টুরিস্ট বাসে গিয়েছিল ভার্সাই। প্রফেসর কার্ল ওর গাড়িটা ব্যবহার করছেন।
***
পরের দিন ক্লাউস একাই বেরিয়েছিল তার গাড়িটা নিয়ে। শহরতলির এক বিশেষ অঞ্চলে। হিটলারের অত্যাচারে দেশত্যাগ করার আগে সে কিছুদিন পারিতে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিল। ওকে যারা আশ্রয় দিয়েছিল তাদের কিছু তত্ত্ব-তালাশ নেবার উদ্দেশ্যে। দেখা পেল না কারও। যুদ্ধের ডামাডোলে ও-অঞ্চলের বাসিন্দারা তো ছাড়, গোটা ভূগোলটাই পালটে গেছে। সব অচেনা মানুষ। হোটেলে ফিরে এসে রিপেসশান কাউন্টারে নিজের ঘরের চাবিটা নিতে যাবে হঠাৎ নিজের নামটা শুনে চমকে উঠল। ওর সামনেই কাউন্টারের দিকে মুখ করে, এবং ওর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছিলেন একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক। কাউন্টারের রিসেপশনিস্ট মেয়েটিকে তিনি বললেন, দেখুন তো ডক্টর ক্লাউস ফুকস-এর নামে কোনো চিঠি আছে? রুম নম্বর 728?
মেয়েটি কাউন্টারের পিছনে পায়রার খোপের মতো একটা বাক্স থেকে বার করে আনল একটা মোটা খাম। তখনই হস্তান্তরিত করল না কিন্তু। বলল, আপনার। চাবিটা প্লিজ?
–ও সার্টেনলি! বৃদ্ধ তাঁর পকেট থেকে হোটেলের চাবিটা বার করে টেবিলে রাখলেন।
মেয়েটি বললে, মাপ করবেন, এটা 729 নম্বর।
বৃদ্ধ যেন চমকে ওঠেন। তারপর হো-হো করে হেঠে ওঠেন। বলেন, আমারই ভুল। প্রফেসর কার্ল-এর ঘরের চাবিটা ভুল করে নিয়ে নিয়ে এসেছি। ওই 728 আর 729 আমি একসঙ্গে বুক করেছি।
মেয়েটি জবাব দেয় না। একটা রেজিস্টার খুলে কী যেন দেখে। তারপর সে নিশ্চিন্ত হয়ে হাসে। ফরাসি ভাষায় বলে, আপনারা, মানে ইংরেজ অধ্যাপকরা, সবাই একরকম। যান, আপনার বন্ধুর চাবিটা তাকে ফেরত দিয়ে আসুন।
বৃদ্ধ অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে খাম আর চাবিটা তুলে নিয়ে সরে পড়লেন। ক্লাউস এতক্ষণে চিনতে পারল তাঁকে। নিঃসন্দেহে তিনি প্রফেসর অটো কার্ল-যদি না তার যমজভাই হন। তফাত শুধু এই প্রফেসর কার্ল এর দাড়ি-গোঁফ পরিষ্কার করে চাছা, এই বৃদ্ধের দিব্যি কঁচাপাকা ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি।
বৃদ্ধের অলক্ষ্যে সে তাকে অনুসরণ করে সদর দরজা পর্যন্ত এল। বৃদ্ধ হন্তদন্ত হয়ে বার হয়ে গেলেন। হোটেলের পোর্টিকোর তলাতেই অপেক্ষা করছিল একটা কালো রঙের মার্সেডিজ। তার ড্রাইভার দরজা খুলে দিল। মুহূর্তমধ্যে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।
ঘটনাটা নিরতিশয় অদ্ভুত। কে ওই বৃদ্ধ? কেন তিনি ক্লাউস ফুকস্-এর নামে মিথ্যা পরিচয় দিলেন মেয়েটির কাছে? গাড়িটাই বা কার? অন্যমনস্কের মতো সে ফিরে এল কাউন্টারে। মেয়েটিকে বললে, নাম্বার 728 প্লিজ?
যান্ত্রিক অভ্যাসে হুক থেকে নামিয়ে মেয়েটি বাড়িয়ে ধরে চাবিটা।
-দেখুন তো 729 নম্বর চাবিটা এখানে আছে কিনা?
হঠাৎ কী মনে পড়ে যায় মেয়েটির। বলে, ও হো! আপনাদের চাবি দুটো উল্টোপাল্টা হয়ে গিয়েছে। আপনার বন্ধু আপনার চাবিটা নিয়ে চলে গেলেন। এইমাত্র…
–ঠিক আছে। একটা ঘরে ঢুকতে পারলেই হল।
নিজের ঘরে ফিরে এসে ক্লাউস আদ্যোপান্ত ব্যাপারটা তলিয়ে দেখে। কী হতে পারে? প্রফেসর কার্ল দুটি ঘর ভাড়া নিয়েছেন; 729 নিজের নামে, 728টা ফুকস-এর নামে। অথচ কাউন্টারে তিনি আত্মপরিচয় দিলেন ডক্টর ফুকস্ বলে। তার ওপর ছদ্মবেশ। প্রফেসর কার্ল একদিন স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাঁর পিছনে গুপ্ত আততায়ী লেগে থাকায় তিনি বিস্মিত নন। কেন? তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিয়ে কার কী লাভ? আচ্ছা, রোনাটা কি সব কিছু জানে? সব কথা। রোনাটাকে খুলে বললে কেমন হয়? কিন্তু সে যদি বিশ্বাস না করে? যদি ভাবে, তার স্বামীর বিরুদ্ধে কতকগুলো মিথ্যে অভিযোগ আনছে সে। প্রমাণ করবে কেমন করে?
হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে উঠল। ক্লাউস সেটা তুলে নিয়ে বললে, হ্যালো?
-তুমি ঘরে ফিরে এসেছ? কতক্ষণ?
–রোনাটা কথা বলছে পাশের ঘর থেকে।
–এইমাত্র। প্রফেসর আছেন?
–না। ও তো সেই সকালেই বেরিয়ে গেছে। এস না এ ঘরে? চল, এখনই কোথাও বের হই! চুপচাপ এমন ঘরে বসে থাকার জন্য পারিতে এসেছি নাকি?
-তুমি তৈরি হয়ে নাও তাহলে।
–এ ঘরে এসে দেখ আমি তৈরি কি না।
নিজের ঘরে তালা দিয়ে ও চলে আসে এ-ঘরে। রোনাটা তৈরি হয়েই বসেছিল। নিখুঁত সেজেছে সে।
-বাস রে! এত সাজের ঘটা?
–বাঃ। ভুলে গেছ? আজ সন্ধ্যার পর ফলি বার্জার-এ যাওয়ার কথা আছে না।
–ও হ্যাঁ, তাই তো! না, না, আমি ভুলিনি। কিন্তু তার তো অনেক দেরি। তুমি বোসো দেখি ওখানে। তোমাকে কয়েকটা জরুরি কথা বলতে চাই
-বল।-রোনাটা তার স্কার্ট সামলে আলতো করে বসে সামনের চেয়ারটায়।
ভুল বুঝো না আমাকে। আমি একটা ব্যাপার কিছুতেই বুঝতে পারছি না..আই মিন, প্রফেসর কালের বিষয়ে। আচ্ছা, তুমি কি সম্প্রতি তাঁর ব্যবহারে কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করেছ?
রোনাটা স্পষ্টই সতর্ক হয়। গম্ভীর হয়ে বলে, বলছি। কী একটা দুশ্চিন্তায় উনি একেবারে মুষড়ে পড়েছেন। আমাকে কিছু বলতে চান না, কিন্তু বেশ বুঝতে পারি, সেই চিন্তাটা ওঁকে কুরে কুরে খাচ্ছে। রাত্রে ঘুমোন না। সারারাত পায়চারি করেন–
-তুমি কি মনে কর প্রফেসরের কোনো শত্রু আছে? কেউ তাকে ব্ল্যাকমেল করছে?
–আমার তো তা মনে হয়নি এতদিন। অমন দেবতুল্য মানুষের শত্রু থাকবে কেন?
ফুকস্ কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবে। তারপর মনস্থির করে বলে, আমি যদি বলি প্রফেসর কার্লকে হত্যা করবার উদ্দেশ্যে একজন আততায়ী সর্বদা ওঁর পেছনে ঘুরছে–বিশ্বাস করতে পার?
অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে রোনাটা। তারপর নীরবে মাথা নেড়ে জানায়না।
ক্লাউস আর দ্বিধা করে না। ওদের সেই দুর্ঘটনার আনুপূর্বিক একটা বনা দেয়। উপসংহারে বলে, প্রফেসর কার্ল আমাকে বারণ করেছিলেন একথা কাউকে জানাতে। আমি কাউকেই বলিনি, অথচ কেমন করে জানি আর্নল্ড সেটা জেনে ফেলেছে। তোমাকেও এতদিন বলিনি। আজ আর একটা ঘটনা ঘটায় মনে হল তোমার জানা উচিত। তাই বললাম। বিশ্বাস করতে পারলে?
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে রোনাটা বললে, তুমি মিছিমিছি আমাকে মিথ্যা কথাই বা বলবে কেন? তাছাড়া আজ বুঝতে পারছি, আর্নল্ড কেন সেদিন আমাকে অত জেরা করছিল।
–কবে? কী জাতীয় জেরা?
-কতকগুলো ফটো দেখিয়ে জানতে চাইল, তাদের আমি চিনি কিনা। লস অ্যালামসে তাদের আমি কখনও দেখেছি কিনা। আমি সবচেয়ে অবাক হলাম যখন আর্নল্ড বললে, আপনাকে যে এসব প্রশ্ন করেছি তা কাউকে বলবেন না। আপনার। স্বামীকেও নয়।
–কেন, তা জানতে চাওনি তুমি?
–চেয়েছিলাম। আর্নল্ড বলেছিল, এটা কার্লের ভালোর জন্যই। কিন্তু তুমি তখন কী বললে? আজ আর একটা ঘটনা কী ঘটতে দেখেছ বলছিলে—
ফুকস্ সরাসরি সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করে, তুমি ডক্টর অ্যালেন নান মে-র নাম শুনেছ?
–শুনেছি। একটা ঘৃণিত বিশ্বাসঘাতক। কাগজে দেখেছি তার জেল হয়েছে। ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল যদিও।
হাসল ফুকস্ ওর উত্তেজনা দেখে। বললে, তুমি ডেক্সটার’-এর নাম শুনেছ?
–কে ডেক্সটার? অনেক ডেক্সটারকেই আমি চিনি। ওটা একটা সাধারণ নাম। কার কথা বলছ তুমি?
ফুকস্ সংক্ষেপে লস অ্যালামসের তথাকথিত প্রতারক ডেক্সটার-এর কথা বলে। ইতিপূর্বে আর্নল্ড এবং তারও আগে লস অ্যালামসে ম্যাককিলভি তাকে যেটুকু বলেছিল সেটুকুও জানায়। শুনতে শুনতে কেমন যেন বিচলিত হয়ে ওঠে রোনাটা। হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, এনাফ। এনাফ অফ ইট। তুমি আজ কী দেখেছ বলো?
ফুকস্ অতঃপর মাত্র আধঘণ্টা আগে যা দেখেছে তার একটা আনুপূর্বিক বর্ণনা দেয়।
রোনাটা বলে, তুমি নিশ্চয় ভুল দেখেছ, ভুল শুনেছ। এ কখনও সত্য হতে পারে। প্রফেসর কার্ল একজন দেবচরিত্রের মানুষ। তুমি তাকে..না, না, ছি, ছি!
ফুকস্ নিজেকে গুটিয়ে নেয়। বলে, তাই হবে–হয়তো ভুলই দেখেছি। ভুলই শুনেছি।
–নিশ্চয়ই। উনি তো সেই সকালে বেরিয়ে গেছেন। তাছাড়া দাড়ি-গোঁফ এঁটে…তোমার মাথা খারাপ!
ফুকস্ উঠে দাঁড়ায়। বলে, কই বের হবে বলেছিলে যে?
-না। মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে। বস তুমি। আচ্ছা, ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলতো জুলি, তুমি নিজে এটা বিশ্বাস করতে পারছ? আমার স্বামী এতবড় বিশ্বাসঘাতক?
ফুকস্ একটুক্ষণ চুপ করে কী যেন ভাবে। তারপর প্রতিটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করে বলে, ঈশ্বরের নামে শপথ আমি নিই না রোনাটা। আমি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না। আমি নাস্তিক।
এবার স্তম্ভিত হবার পালা রোনাটার। অনেকক্ষণ নির্নিমেষ নয়নে সে তাকিয়ে থাকে ওর মুখের দিকে। তারপর অদ্ভুত স্বরে বললে, এ সব কী বলছ জুলি! তুমি নাস্তিক?
-হ্যাঁ তাই।
–আজ বিশ বছর মেলামেশার পর তুমি আমাকে একথা বিশ্বাস করতে বলো?
–বলি। এতদিন তোমাকে সাহস করে জানাইনি।
–আজই বা তাহলে জানালে কেন?
-আমার মনে হচ্ছে, তোমার-আমার শেষ বোঝাঁপড়ার দিন এসে গেছে। তোমার-আমার শেষ সিদ্ধান্তের আগে সবকিছু তোমার জেনে নেওয়া দরকার।
–শেষ সিদ্ধান্তটা কীসের?
–প্রফেসর কার্লকে যদি ডিভোর্স করতে বাধ্য হও তারপর…
রোনাটা একখানা হাত বাড়িয়ে দেয়। থামতে বলছে ওকে। ফুকস্ কিন্তু থামে না। বলে, থামবার উপায় নেই রোনাটা। এই হচ্ছে বাস্তব অবস্থা। আমি ও ঘরে চলে যাচ্ছি। যদি মনটা স্থির হয়, বের হবার ইচ্ছে হয়, আমাকে ফোন কোরো বরং…
***
নিজের ঘরে ফিরে এসে কাবার্ড থেকে বের করে হুইস্কির বোতলটা। মনটা আজ অনেক হালকা বোধ হচ্ছে। এতদিনে সে মন খুলে সত্যি কথাটা বলে ফেলেছে। সে নাস্তিক। এটাই ছিল রোনাটার সঙ্গে তার মিলনের পথে অন্যতম প্রধান বাধা। রোনাটা ধর্মভীরু, তার বাপের মতো। ক্লাউস মনে করে ঈশ্বর একটা ভাওতা। কতকগুলো ফন্দিবাজ লোকের একটা ফাঁকিবাজি। সাহস করে এতদিন রোনাটাকে কথাটা বলতে পারেনি। আজ মনের ভার নেমে গেছে। হঠাৎ ওর মাথায় একটা ফন্দি জাগে। প্রফেসর কার্লকে একটু বাজিয়ে দেখতে দোষ কী? ছদ্মবেশি লোকটা আসলে কে, সে কথা তাহলেই সহজে বোঝা যাবে। চট করে টেবিল থেকে একটা সাদা কাগজ তুলে নেয়। বাঁ-হাতে কলমটা ধরে ক্যাপিট্যাল অক্ষরে বড় বড় করে লেখে, “ছদ্মবেশ এবং ছদ্মনাম সত্ত্বেও তোমাকে কিন্তু চিনতে পেরেছি।”
কাগজটা ভাজ করে একটা খামে বন্ধ করে। উপরে লেখে ‘ডক্টর ক্লাউস ফুকস, রুম নং 728’। তারপর ঘরে চাবি দিয়ে নেবে যায় নীচে। রিসেপশান-কাউন্টারে এসে দেখে মেয়েটি চলে গেছে। তার বদলে অন্য একটি ছেলে বসে আছে। তার হাতে খামটা দেয়। যন্ত্রচালিতের মতো ছেলেটি পিছনের নম্বরি খোপে চিঠিখানা রেখে দেয়।
ফুকস্ আবার ফিরে আসে ওর ঘরে। বোতলটা টেনে নেয়। রেডিওটা খোলে। উৎকট জ্যাজ বাজছে কোথাও। বন্ধ করে দেয়। পাত্রটা হাতে উঠে গিয়ে দাঁড়ায় জানলার পাশে। নীচে প্রবহমান পারির সন্ধ্যা। গাড়ির ক্যারাভান আর নিওন আলোর ঝলকানি। বারে, পাবে, স্ট্রিপটিজ নাচের আসরে নিচের তলায় পারি এতক্ষণে জমজমাট। আর ও একা ঘরে বসে মদ্যপান করছে। পাশের ঘরেও নিশ্চয় বসে আছে কাঠ হয়ে অধ্যাপকের শুচিবায়ুগ্রস্ত ধর্মপত্নী-স্বামীর সঙ্গে যার বাইশ বছর বয়সের ফারাক। ‘দুত্তোর’ বলে উঠে পড়ে ক্লাউস। ঢকঢক করে পাত্রের বাকি মদটুকু ঢেলে দেয় গলায়। হাতের উল্টোপিঠে মুখটা মুছে নেয়। তারপর ঘর বন্ধ করে চলে যায় আবার পাশের ঘরে।
কিন্তু দ্বারের সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। ঘরের ভেতর বচসা হচ্ছে। দাম্পত্যকলহ নিশ্চয়, অর্থাৎ অধ্যাপক-মশাই ফিরে এসেছেন এতক্ষণে। কী। কথা হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না–কিন্তু দুজনেই উত্তেজিত। পায়ে পায়ে আবার ফিরে আসে নিজের ঘরে।
আবার হুইস্কির বোতলটা টেনে নেয়।
***
ঘণ্টাতিনেক কেটে গেছে তারপর। বোতলটা কখন জানি শেষ হয়ে গেছে। তখনও ওর তৃষ্ণা মেটেনি। হুইস্কিতে এ তৃষ্ণা মিটবে না বোধহয়। নৈশাহার হয়নি। ফলি বার্জার-এ নৈশাহারের জন্য টেবিল বুক করা ছিল। যায়নি। এখন কিন্তু খেতে যাবার মতো শারীরিক অবস্থাও আর নেই। রীতিমতো পা টলছে। জামা কাপড় ছেড়ে নৈশসজ্জা পরে নেয়। তারপর নীল বাতিটা জ্বেলে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে। ঘুম আসে না কিছুতেই।
অনেক পরে মনে হল কে যেন দ্বারে সন্তর্পণে টোকা দিচ্ছে। ফুকস্ বিরক্ত বোধ করে। দ্বারের বাইরে সে বোর্ড টাঙিয়ে দিয়েছে ‘বিরক্ত করবেন না’–তবু কে এল জ্বালাতে? টলতে টলতে এসে দরজা খুলে দিয়েই চমকে ওঠে একেবারে।
করিডোরে স্তিমিত আলোয় দাঁড়িয়ে আছে বোনাটা।
সন্ধ্যার সেই সাজসজ্জা নেই তার অঙ্গে। পরেছে একটা নাইটি। অদ্ভুত বিচিত্র বর্ণের সেই ঢিলে-ঢালা পোশাকটা। ধূসর রঙের সঙ্গে এসে মিশেছে কিছুটা সিঁদুরে লাল, কিছুটা বা হলুদ, কমলা অথবা নীল। এমন বর্ণসম্ভার সে কোথায় যেন দেখেছে! রামধনু রঙে? প্রজাপতির পাখায়? সূর্যাস্তের বর্ণসম্ভারে? ঠিক মনে পড়ছে না। হুইস্কির একটা তরল পর্দা ওর স্মৃতিপথে যবনিকার সৃষ্টি করেছে!
-তুমি!
নিঃশব্দে রোনাটা ঢুকে পড়ে ওর ঘরে। দরজাটা ঠেলে দেয়। ইয়েল-লক। তৎক্ষণাৎ তালাবন্ধ হয়ে গেল নিশ্চয়। ঘরটা ছিল আলো-আঁধারী। নীলাভ আলোর একটা মোহময় আবরণে ঢাকা। রোনাটা হাত বাড়িয়ে টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে দেয়। হঠাৎ আলোর বন্যায় চোখ ধাঁধিয়ে গেল ক্লাউস-এর। ওর মনে হল রোনাটা নাইটির নীচে অধোবাস পরেনি। ওর অন্তরের যুগ্মকামনা উত্তুঙ্গ হয়ে উঠেছে। রোনাটা কিন্তু তার বেশবাস বিষয়ে সচেতন নয়। এসে বসল সে চেয়ারটা টেনে নিয়ে। একখানা কাগজ বাড়িয়ে ধরে বললে, পড়ে দেখ।
-কী ওখানা?-কাগজটা হাত বাড়িয়ে নেয়।
–একটু আগে হোটেলের একজন বয় দিয়ে গেল।
প্রফেসর অটো কার্ল-এর সংক্ষিপ্ত পত্র। স্ত্রীকে লেখা। সম্বোধনবিহীন। লিখেছেন, বিশেষ জরুরি প্রয়োজনে তিনি কর্মস্থলে ফিরে যাচ্ছেন। রোনাটা যেন ক্লাউসের সঙ্গে পরে সুবিধামতো ফিরে আসে। ব্যস। আর কিছু নয়।
-কী হতে পারে বল তো?
ফুকস্ প্রশ্নটা এড়িয়ে বলে, ওঁর সঙ্গে আর দেখা হয়নি তোমার?
হয়েছিল। ঘণ্টাখানেক আগে এসে খামকা আমার সঙ্গে ঝগড়া করে গেছেন। বললেন, আমি নাকি ওঁকে চিঠি লিখে ভয় দেখাচ্ছি।
–কী চিঠি?
–কী জানি। কিছুই খুলে বললেন না।
–কী করবে এখন?
–তাই তো পরামর্শ করতে এলাম তোমার সঙ্গে।
–আমার সঙ্গে? আমার পরামর্শ তুমি শুনবে?
–কেন শুনব না?
–আমি যে নাস্তিক। আমি যে বিশ্বাসঘাতক।
-প্লিজ, অমন করে বোলো না। তোমাকে আমি কোনোদিনই বিশ্বাসঘাতক বলিনি।
–কিন্তু আমিও তো বিশ্বঘাতক হয়ে উঠতে পারি?
–না, পার না।
–পারি না? প্রফেসর কার্ল বিশ্বাস করে তার সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে এভাবে ফেলে পালাতে পারেন, তুমি এমন নাইটি পরে এতরাত্রে অসঙ্কোচে ব্যাচিলারের ঘরে আসতে পার, আর আমিই শুধু বর্বর হয়ে উঠতে পারি না?
-না পার না, জুলি। কারণ তুমি জান তাহলে আমি আত্মহত্যা করব। আমি খ্রিস্টান, আমি বিবাহিতা। আমি ব্যভিচারিণী হতে পারি না।
ক্লাউস নিরুদ্ধ আক্রোশে বিছানার ওপর একটা ঘুষি মারে।
রোনাটা হেসে বলে, পুয়োর চাইল্ড।
–থাক। রসিকতা কোরো না।–আবার উঠে যায় কাবারে কাছে। আর একটা বোতল পেড়ে আনে।
রোনাটা বলে, আর খেও না। তোমার পা টলছে।
-তুমি পাষাণ।
–আর তুমি নাস্তিক। কিন্তু নাস্তিকদেরও একটা জিনিস থাকে জুলি–’কোড অফ এথিক্স’।
–কিন্তু আমি তো মানুষ?
–তাই তো সেদিন বলছিলাম-তুমি বিয়ে করো। সংসার করো।
–আর তুমি? তোমার কী হবে?
–আমার আবার কী হবে?
–তুমি এমন দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছ কেন? নিজের চিকিৎসা করাচ্ছ না কেন?
ম্লান হাসল রোনাটা। ফুকস দু-পাত্র তরল পানীয় ঢালল। তারপর বললে, কই, জবাব দিলে না?
–কী জবাব দেবো? এ রোগের চিকিৎসা নেই, আমি জানি।
–কী রোগ?
–এখন আর তো তোমাকে জানানো যাবে না।
–কেন?
–নাস্তিককে তা বলা যায় না।
পানীয়টা কণ্ঠনালীতে ঢেলে দিয়ে আবার এক পাত্র ঢালে। বলে, বলতে তোমাকে হবে না। আমি জানি, কী তোমার রোগ। কী তার চিকিৎসা।
কৌতুক উপচে পড়ল রোনাটার গলায়। বললে, তাই নাকি? শুনি একটু।
–তোমার ‘মা’ হওয়া দরকার। তুমি একজন গাইনোকলজিস্টকে দিয়ে নিজেকে দেখাও।
রোনাটা জবাব দেয় না। এতক্ষণে পানপাত্রটা তুলে নেয় হাতে। এক সিপ মুখে দিয়ে বলে, তার প্রয়োজন নেই। আমার কোনো আঙ্গিক ত্রুটি নেই।
তবে কি প্রফেসর?
এবারও ইতস্তত করে রোনাটা জবাব দিতে। তার হাতটা কাঁপছে। সেই সঙ্গে কাঁপছে তার হাতে তরল পানীয়টা। অনেকটা খেয়ে ফেলে একসঙ্গে। মুখটা মুছে নিয়ে বলে, এসব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা কি তোমার উচিত হচ্ছে?
ফুকস্ খাটের প্রান্তে এগিয়ে আসে। রোনাটার কাঁধে একখানা হাত রাখে। বলে, হচ্ছে রোনাটা। আমার সে অধিকার আছে। তবে কি প্রফেসরই দায়ী?
-প্লিজ। আমাকে জিজ্ঞাসা কোরোনা, আমি বলতে পারব না।
দু-হাতে মুখ ঢাকে রোনাটা। ফুকস্ দু-হাতে ওর অনাবৃত বাহুমূল শক্ত মুঠিতে ধরে একটা ঝাঁকানি দেয়, বলে–বলতে তোমাকে হবেই রোনাটা। প্রফেসর কি পিতা হবার উপযুক্ত নন?
তবু মুখ থেকে হাত সরায় না রোনাটা। তার সোনালি চুলে ভরা মাথাটায় একটা ঝাঁকি দিয়ে বলে, আমি জানি না। বিশ্বাস করো, আমি জানি না।
-তবে কোনো ডাক্তারের কাছে তাকে নিয়ে যাওনি কেন?
হঠাৎ হাত সরে গেল রোনাটার। অশ্রুআর্দ্র দুটি চোখের দৃষ্টি মেলে ধরে বলে,
–বিশ্বাস করবে জুলি? অ্যালিসের মা এটাকে মেনে নিতে পারেনি। সে…অন্যত্র সান্ত্বনা খুঁজত।
-তার মানে? সব কথা আমাকে বল দেখি?
কিন্তু সব কথা খুলে বলা যায়? ওর কাছেও? হঠাৎ একেবারে ভেঙে পড়ে রোনাটা। উপুড় হয়ে পড়ে ওর বালিসের ওপর। ফুকস্ ওর প্ল্যাটিনাম-বুন্ড চুলের। ওপর ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে দেয়। সে স্পর্শে একবার শিউরে উঠে রোনাটা। তার পিঠটা থরথর করে কাঁপতে থাকে। তারপর ওইভাবে মুখ লুকিয়েই বলে, বিবাহের আগেই প্রফেসর আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার সন্তানের মা হতে হবে না আমাকে!
হঠাৎ জোর করে ওকে টেনে তোলে! দু-হাতে ওর বাহুমূল শক্ত করে ধরে মুখোমুখি বসিয়ে দেয়। বলে, প্রতিশ্রুতি! কীসের জন্য প্রতিশ্রুতি! তুমি চেয়েছিলে? কেন?
–তাও কি বলে দিতে হবে তোমাকে?
চোখ দুটো জ্বলে ওঠে মাতালটার। বলে, তুমি কি পাগল? আমার জন্যে!!
হঠাৎ ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেলে রোনাটা। থরথরিয়ে কেঁপে ওঠে ওর ঠোঁট দুটো। অস্ফুটে বলে ফেলে, উড য়ু বিলিভ মি, জুলি, অ্যাট দিস এজ, আফটার এইট ইয়ার্স অব ম্যারেড লাইফ..আই অ্যাম,…ইয়েট, ইয়েট–এ ভার্জিন।
–”ফোর…থ্রি..টু…ওয়ান…নাউ!
“প্ৰকাণ্ড একটা ধোঁয়ার বলয় পাক খেতে খেতে ওপরে উঠে যাচ্ছে। ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ওপর আর একটা আগুনের বলয়–তার কিনারাগুলো সিঁদুরে লাল। ওপরে ওপরে, আরও ওপরে উঠে গেল। অনাবিষ্কৃত একটা নগ্নসত্য আবির্ভূত হল ওর চোখের সামনে। পারমাণবিক বন্ধনমুক্ত মহামৃত্যু নেমে এল এবার পৃথিবীর বুকের ওপর।
“তারপর অস্বাভাবিক একটা নিস্তব্ধতা। পুরো দেড় মিনিট কেউ কোনো কথা বলেনি।”
.
০৭.
পরদিন অনেক বেলায় ফুকস-এর যখন ঘুম ভাঙল তখনও ওর মাথাটা ভার। কাল রাত্রের কথা আবছা মনে পড়ছে। কী যেন ঘটেছিল? কে যেন এসেছিল ওর ঘরে? একে একে সব কথা মনে পড়ে যায়। কখন পাশের ঘরে উঠে চলে গিয়েছিল রোনাটা? মনে পড়ছে না। মুখ হাত ধুয়ে নিল প্রথমেই। তারপর জামাকাপড় বদলে ফোন করল পাশের ঘরে। ফোন বেজেই গেলো। ধরল না কেউ। কী ব্যাপার? নিশ্চয় রোনাটা ঘুমাচ্ছে এখনও। তা তো হতেই পারে, ত্রিশ বছরের জীবনে এমন একটা রাত তার অভিজ্ঞতায় এই প্রথম।
আরও ঘন্টাখানেক পরে আবার ফোন করল। এবারও নিরুত্তর।
খোঁজখবর নিতে গিয়ে যা জানা গেল তা প্রায় অবিশ্বাস্য। মিসেস রোনাটা কার্ল ভোরবেলা উঠে হোটেল থেকে চেক-আউট করে বেরিয়ে গিয়েছেন। ঠিকানা রেখে যাননি।
একটা দিন অপেক্ষা করল। যদি অন্য কোনো হোটেল থেকে রোনাটা ফোন করে। তারপর হারওয়েলে ফিরে গেল সে দ্বিতীয় দিন।
সেখানে তার জন্য প্রতীক্ষা করছিল সবাই।
অদ্ভুত খবর। দুদিন আগে মিসেস অটো কার্ল ফিরে এসেছিলেন। পাড়ার লোক শুনেছে–স্বামী-স্ত্রীতে প্রচণ্ড ঝগড়া হয়েছিল রাত্রে। সকালবেলা জানা গেছে। অধ্যাপকজায়া আত্মহত্যা করেছেন। ফুকস্ যখন ফিরে এল তখনও মৃতদেহের সকার হয়নি।
ক্লাউস ফুকস-এর মানসিক অবস্থাটা সহজেই অনুমেয়। রুদ্ধদ্বারকক্ষে একা বসে রইল সে সারাটা দিন। প্রফেসর কার্ল-এর চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারল না। কতটা জানেন তিনি? কতটা বলে ফেলেছে রোনাটা? এমনটা যে হবে, তা কে ভেবেছিল? সে বসে বসে সে-রাত্রের কথাটা ভাবেনাঃ। সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে রোনাটাকে বাধ্য করেনি। অত বড় জানোয়ার সে নয়। মনে পড়ে যায় অনেক অনেকদিন আগেকার সেই কথা। সেদিনও ওর চুম্বন-উদ্যত আনত মুখটা। ঠেলে দিতে চেয়েছিল প্রথমে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত দৃঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরেছিল ওকে। ঠিক সেই অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি কি আবার হয়নি এবার? তাহলে এমন কাণ্ডটা কেন করল রোনাটা? তবে কি হেতুটা ক্লাউস নিজে নয়–প্রফেসর কার্ল? রোনাটা কি বুঝতে পেরেছে, প্রফেসর কার্ল এ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক? দেশের প্রতি, মুক্ত পৃথিবীর প্রতি জঘন্যতম অপরাধ করেছে যে-মানুষটা তার সহধর্মিণী হয়ে বেঁচে থাকতে চায় না রোনাটা।
হঠাৎ ঝনঝন করে বেজে উঠল টেলিফোনটা।
মদের পাত্রটা নামিয়ে রেখে ক্লান্ত ফুকস্ টেলিফোনটা তুলে নেয়। সিকিউরিটি অফিসার জেমস্ আর্নল্ড একবার দেখা করতে চান। অবিলম্বে। ফুকস্ রীতিমতো বিরক্তি প্রকাশ করে বললে, মাপ করবেন, আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। আজ আমি কোনো কথা বলতে পারব না।
–আপনিই বরং মাপ করবেন আমাকে। আপনার মানসিক অবস্থাটা বুঝতে পারছি। ডক্টর, কিন্তু আমি নিরুপায়। ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরি। আমি একবার আসছি।
পুলিসের লোক। ’না’ বললে শোনে না। ওরা মানুষের সুখ-দুঃখ-অনুভূতির ধার ধারে না।
একটু পরেই এসে উপস্থিত হল জেমস্ আর্নল্ড। বললে, আমি জানি মিসেস কার্ল ছিলেন আপনার বাল্যবান্ধবী। তার এমন পরিণামে আপনি যে কতটা মর্মাহত তা অনুমান করতে পারি। কিন্তু ইতিমধ্যে এমন কতকগুলি ব্যাপার ঘটেছে যাতে আপনাকে বিরক্ত করতে বাধ্য হচ্ছি।
ফুকস্ পানীয়টুকু গলাধঃকরণ করে বললে, বলুন। আমি প্রস্তুত।
-পারিতে অথবা পথে কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটতে দেখেছেন আপনি?
অম্লানবদনে ফুকস্ বললে, না, তেমন কিছু তো আমার নজরে পড়েনি।
মিসেস কার্ল কেন আত্মহত্যা করলেন কিছু অনুমান করতে পারেন?
–না।
-ফর য়োর ইনফরমেশন ডক্টর, ঘটনার পূর্বদিন রাত্রে কলহের সময় ওঁরা বার বার যে শব্দটা উচ্চারণ করেছিলেন, রুদ্ধদ্বার কক্ষের বাইরে তা মনে হয়েছে-ট্রেইটার, বিশ্বাসঘাতক।
ফুকস্ নির্লিপ্তের মতো বললে, দাম্পত্য-কলহে ও শব্দটা এমন কিছু অপ্রত্যাশিত নয়। যে কোনো পক্ষ যখন মনে করে অপরপক্ষ তার প্রেমের মর্যাদা দিচ্ছে না তখন ওই শব্দটা ব্যবহার করে।
আর্নল্ড ঘরোয়া হতে চায়। হেসে বলে, আপনি ব্যাচিলার হয়েও তো অনেক খবর রাখেন।
ফুকস্ কিন্তু হাসে না। নীরবে আর এক পাত্র মদ ঢালতে থাকে।
-কিন্তু ব্যাপারটার ওখানেই শেষ হয়নি ক্লাউস ফুকস। পরদিন ওঁদের মেডসার্ভেন্ট ডরোথি যখন প্রশ্ন করে গৃহকর্ত্রী এমনভাবে আত্মহত্যা করলেন কেন, তখন অসতর্ক মুহূর্তে প্রফেসর বলেছিলেন-রোনাটা বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে ঘর করতে চায় না বলে।
ফুকস্ চমকে ওঠে। বলে, বলেন কী। তারপর? প্রফেসর এ কথার কী জবাবদিহি করছেন?
করছেন না। তিনি কোনো জবানবন্দি দেননি এবং দেবেন না বলেছেন।
–আই সি।
আর্নল্ড এতক্ষণে বোতল থেকে নিজের পাত্রে মদ ঢালে। আরও ঘনিয়ে বসতে চায় সে। প্রশ্ন করে, আপনি অমনভাবে চমকে উঠলেন কেন ডক্টর?
–চমকে উঠলাম? কই না তো? চমকে উঠব কেন?
–আমার মনে হল যেন আপনি বলতে চাইছেন মিসেস কার্ল শুধু দাম্পত্য জীবনের বিশ্বাসঘাতকতার প্রসঙ্গে কথা বলেননি।
ফুকস্ জবাব দেয় না। সে আরও সতর্ক হয়ে ওঠে।
–আর একটা কথা। পারির হোটেলে কি আপনি এমন একজন বৃদ্ধকে দেখেছিলেন, যাঁকে দেখতে অবিকল প্রফেসর কার্লের মতো, অথচ তার ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি আছে?
অম্লানবদনে ফুকস বললে, কই না তো।
–রোনাটা মারা যাবার পর প্রফেসরের সঙ্গে আপনার কথা হয়েছে?
হয়েছে। মামুলি সান্ত্বনার কথা ছাড়া আর কিছুই আলোচনা হয়নি।
হঠাৎ কেন উনি পারি থেকে হারওয়েলে ফিরে এলেন তা জানাননি?
-না। প্রশ্নটা করবার অবকাশ পাইনি। উনি আর একটু মানসিক স্থৈর্য ফিরে পেলে জিজ্ঞাসা করব।
করবেন। তিনি কী বলেন জানাবেন আমাকে।
–জানাব।
***
ওকে প্রশ্ন করতে হয়নি। প্রফেসর নিজেই বলেছিলেন। রোনাটাকে সমাধিস্থ করার পরে একদিন প্রফেসর কার্ল এসে দেখা করলেন ফুকসের সঙ্গে। বললেন, তুমিই এবার হারওয়েলে নাম্বার ওয়ান হলে। স্যার জন কক্ৰক্ট অবসর নিচ্ছেন শুনেছ নিশ্চয়, আর আমিও পদত্যাগ করছি।
–পদত্যাগ করছেন? আপনি। কেন?
–আমি চিরদিনের জন্য হারওয়েল ছেড়ে চলে যাচ্ছি, ক্লাউস।
–কেন স্যার?
–তোমাকে তো আগেই বলেছি জুলি–প্রত্যেক ক্রিশ্চিয়ানের জীবনে এমন একটা ‘ক্রস্’ থাকে যার ভার তাকে নিজেকেই বইতে হয়।
–আমাকে সব কথা খুলে বলবেন?
-বলতেই তো এসেছি। তবে সব কথা নয়। কারণ সবটা আমার নিজের কথা নয়–
-তবে কার? রোনাটার?
-না, আমার যমজ-ভাইয়ের। রোনাটার সব কথা তোমাকে খুলে বলতে আমার আপত্তি নেই। সে কথা শোনার অধিকার তোমার আছে। কী জানতে চাও বলো?
ফুকস্ কোন ইতস্তত করল না। সরাসরি চরম প্রশ্নটা একেবারে প্রথমেই পেশ করে বসে, রোনাটা আপনার সন্তানের জননী হয়নি কেন? অসুস্থ ছিল কে? আপনি না রোনাটা?
বৃদ্ধ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বিদ্ধ করেন প্রশ্নকারীকে। প্রতিপ্রশ্ন করেন, রোনাটা বলেনি তোমাকে?
–না। সে শুধু বলেছিল–বিবাহের আগেই আপনি নাকি কথা দিয়েছিলেন, আপনার সন্তানের জননী হতে হবে না তাকে।
-হ্যাঁ, ঠিক কথা। ওইরকম একটা প্রতিশ্রুতি আমি দিয়েছিলাম।
–কিন্তু কেন? কেন?
-কারণ কোনো সন্তানের পিতা হবার মতো শারীরিক ক্ষমতা আমার নেই। অ্যালিসের মাকে বিবাহ করে সেটা বুঝতে পেরেছিলাম আমি।
ফুকস্ অসহিষ্ণুর মতো মাথা ঝাঁকিয়ে চাপা আর্তনাদ করে ওঠে, তবে সব জেনেশুনে কেন ওই বাইশ বছরের মেয়েটির এতবড় সর্বনাশ আপনি করলেন? এজন্য পরলোকে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে না?
ম্লান হাসলেন কার্ল। বললেন, পরলোক। তুমি মানো?
-না, মানি না, আমি মানি না, কিন্তু আপনি তো মানেন। এজন্য নিজেকে দায়ী। মনে করেন না?
শান্ত সমাহিত কণ্ঠে অধ্যাপক বললেন, না। এজন্য আমি দায়ী করি তোমাকে।
–আমাকে?
–হ্যাঁ, তোমাকে। এবার তুমি জবাবদিহি কর কেন ওই বাইশ বছরের মেয়েটার এতবড় সর্বনাশ করলে তুমি? কেন তাকে বিবাহ করনি? কেন তাকে বাধ্য করলে আমার সঙ্গে এমন অস্বাভাবিক জীবন যাপন করতে?
ক্লাউস দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে রইল। জবাব জোগালো না তার মুখে।
বৃদ্ধ তখন একে একে বলতে থাকেন তার অভিজ্ঞতার কথা। অসঙ্কোচে। যেন চার্চে এসে ‘কনফেস্’ করছেন। যেন ক্লাউস ওখানে উপস্থিত নেই। তিনি তাঁর বিচারকের সামনে সব কিছু মনের ভার উজাড় করে দিচ্ছেন :
যৌবনের ঊষাযুগে একটি কলেজে-পড়া প্রাণচঞ্চল মেয়ে ভালোবেসেছিল একটি যুবককে। একই বাড়িতে থাকে ওরা, একই বয়সী প্রায়। ওদের মন জানাজানি হল। তারপর ছেলেটি হঠাৎ একদিন বাঁধন ছিঁড়ে সরে পড়তে চাইল। মেয়েটি প্রাণপণ বলে তাকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল–নির্লজ্জের মতো বলেছিল, আমায় বিবাহ করো। ছেলেটি শোনেনি। প্রত্যাখ্যান করার একটা মনগড়া কৈফিয়ও দেখায়নি। পাথরের দেয়ালে মাথা খুঁড়ে ফিরে এসেছিল মেয়েটি। তারপর অনেক। পুরুষ এসেছে তার জীবনে, কিন্তু সে তার প্রথম প্রেমকে ভুলতে পারেনি। বাবা মারা গেলেন–ভাইবোনেরা প্রতিষ্ঠিত হল জীবনে, বিয়ে করল। ও স্থির করল–আজীবন বিবাহ করবে না। সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবে। নান’ হয়ে যাবে। কিন্তু সেই সংকল্পটাও তার হারিয়ে গেল, যখন অ্যালিসের মা ছয়মাসের শিশুকন্যাটিকে রেখে মারা গেলেন। পিতৃবন্ধু আত্মভোলা অধ্যাপক অটো কার্লকে দেখে মায়া হল মেয়েটির। মা-হারা মেয়েটিকে সে বুকে তুলে নিল। সে নিজেই হতে চাইল অ্যালিসের মা। প্রফেসর কালই বরং আপত্তি করেছিলেন। বয়সের পার্থক্যের জন্য নয়, যৌনজীবনে তিনি যে অশক্ত তা বুঝতে পেরেছিলেন অ্যালিসের মাকে বিবাহ করে। সত্যাশ্রয়ী প্রফেসর নির্দ্বিধায় সব কথা খুলে বলেছিলেন রোনাটাকে। পরিবর্তে রোনাটাও খুলে বলেছিল তার জীবনের গোপনতম লজ্জার কথাটা। সে প্রত্যাখ্যাতা। বলেছিল, প্রফেসর, সন্ন্যাসিনী হতে চেয়েছিলাম আমি, তা এও তো একরকম সন্ন্যাসিনীর জীবন। অন্তত–দুজনেই নিঃসঙ্গতার হাত থেকে তো মুক্তি পাব। আপনার বিধবা মেয়ে থাকলেও তো তাকে বাড়িতে থাকতে দিতেন।
বৃদ্ধ চুপ করলেন। ফুকস্ তখনও বসে আছে স্থাণুর মতো। কিন্তু রেহাই দিলেন না তাকে অধ্যাপক কার্ল। বললেন, সত্যি করে বল তো জুলি, কেন প্রত্যাখ্যান করেছিলে তাকে?
ফুকস উঠে দাঁড়ায়। নীরবে পায়চারি করে কয়েকবার। তারপর বলে, প্রফেসর। প্রত্যেকের জীবনেই এমন একটা ‘ক’ থাকে যার ভার তাকে একাই বইতে হয়–
চীৎকার করে ওঠেন বৃদ্ধ : না। ওকথা বলার অধিকার তোমার নেই। ওটা ক্রিশ্চিয়ানের কথা। তুমি খ্রিস্টান নও। তুমি নাস্তিক। ক্রস’ বইবার অধিকার তোমার নেই।
-আমি নাস্তিক। কে বলেছে আপনাকে?
প্রফেসর কার্ল নীরবে একটি ভোলা চিঠি বার করে ওর হাতে দিলেন। রোনাটার পত্র। শেষ পত্র। লিখে গেছে তার স্বামীকে। সম্বোধন করেছে, ‘মাই ডিয়ার ওল্ড ড্যাডি’ বলে। অকপটে সে স্বীকার করেছে তার পারির শেষ রজনীর অভিজ্ঞতা। সবিস্তারে। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। লিখেছে, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি এ দুর্ঘটনা ঘটত তাহলে নিজেকে ক্ষমা করতাম। তাহলে মিসেস অটো কার্লের পরিচয় বহন করেই জীবনের বাকি কটা দিন কাটিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু তা তো হয়নি। আই ওয়াজণ্ট রেপড। আই কোয়াপরেটেড। অ্যান্ড আই এঞ্জয়েড দ্য অর্গাজম। দ্যাটস্ হোয়াই আই হ্যাভ সিনড।
বুকের ভিতর মুচড়ে উঠল ফুকস-এর। রোনাটা আত্মহত্যা করেনি–ক্লাউস তাকে হত্যা করেছে! মাথাটা সে আর তুলতে পারে না।
–ইউ নিডন্ট ব্লাশ, মাই বয়। আমি অস্বাভাবিক কিন্তু তোমরা দুজনে যা করেছ তাই তো স্বাভাবিক। টেক ইট ইজি।
তাই কি নেওয়া যায়? দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে থাকে ফুকস।
প্রফেসর অন্যমনস্কের মতো বলেন, রোনাটাকে আমি ভালোবাসতাম। প্রয়োজনে প্রটেস্টান্ট হয়েও তার মুখ চেয়েই তাকে ডিভোর্স করবার সংকল্প করেছিলাম। কথাটা তাকে বলা হয়নি। তোমাদের মন জানাজানির একটা সুযোগ করে দেবার জন্যই এভাবে একা পালিয়ে এসেছিলাম পারি থেকে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না–
ফুকস্ এবার মুখ থেকে হাতটা সরায়। আর্তকণ্ঠে বলে, প্লিজ প্রফেসর। আমি একটু একা থাকতে চাই।
তৎক্ষণাৎ উঠে পড়েন অধ্যাপক। পকেট থেকে একটি দেশলাই বার করে জ্বালেন। এক মিনিটের ভিতরেই রোনাটার শেষ পত্রখানি অঙ্গারে পরিণত হল।
***
এর পরের অধ্যায়টা করুণ।
ক্লাউস ফুকস-এর পরিবারে একাধিক লোক যে পাগল হয়ে গিয়েছিল, এতদিন পরে সে কথা মনে পড়ল তার। ওও কি পাগল হয়ে যাচ্ছে? কারা যেন ওর চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। তারা কথা বলে। কী বলে তাও বুঝতে পারে না। ও তাদের সঙ্গে তর্ক করে। বাড়ি ছেড়ে কোথাও যায় না। কারও সঙ্গে মন খুলে কথা বলে না। আর্নল্ড মাঝে মাঝে আসে। বিরক্ত করে। একদিন এসে বললে, আমি নিশ্চিন্তভাবে জানি, প্রফেসর কার্ল আপনাকে রোনাটার শেষ পত্রখানা। দেখিয়েছিলেন। অস্বীকার করতে পারেন?
চীৎকার করে ওঠে ফুকস, হা, দেখিয়েছিলেন। কী হয়েছে তাতে?
–হয়নি কিছু। কী ছিল সেই চিঠিতে? বিশ্বাসঘাতক কে? কীসের? কেন?
–বলব না। প্রফেসর কার্ল ইংল্যান্ড ছেড়ে যাবার পাসপোর্ট পেলেন না। সব কথা খুলে না বলা পর্যন্ত তাকে নজরবন্দি করে রাখা হল সমুদ্র-মেখলা গ্রেট ব্রিটেনের মুক্ত কারাগারে। ছায়ার মতো গুপ্তচর ঘুরছে তার পিছনে দিবারাত্র। আর একটি প্রমাণ, একটি ইঙ্গিত পেলেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে। ডেক্সটাররূপে তাঁকে শনাক্ত করা যাবে। তার আর দেরি নেই। ইলেকট্রিক-চেয়ার আর প্রফেসর কার্ল-এর মধ্যে বৈদ্যুতিক তারের সামান্য একটু ফাঁক। তবু উনি অনমিত। কোনো জবানবন্দি দেবেন না, কোনো স্বীকৃতি জানাবেন না। না, ডেক্সটার কে তা উনি জানেন না। অ্যাটমিক-এনার্জির গুপ্তচরদলের কোনো সংবাদই তিনি রাখেন না। তাঁর পদত্যাগপত্র গৃহীত হল অবশ্য। এখন ব্যাঙ্কের জমানো অর্থই বাকি জীবনের পাথেয়। এ অবস্থায় কে তাকে নতুন চাকরি দেবে?
ফুকস্ আবার অনুভব করে তার চতুর্দিকে অদৃশ্য চক্ষুর মিছিল এসে জুটেছে। দিবারাত্রি কারা যেন তাকে পাহারা দিচ্ছে। দিক। সে ক্ষেপ করে না। সে কোনো কথা স্বীকার করবে না। কারও কাছে নয়। কিন্তু রোনাটা? তার কাছে যে একটা কৈফিয়ৎ আজও দেওয়া হয়নি।
স্লিপিং পিল আর মদের মাত্রা বাড়ল। তবু ঘুম আসে না। জীবনের উদ্দেশ্যটাই বুঝি হারিয়ে গেছে। কী হবে বেঁচে থেকে? এভাবে বেঁচে থেকে? ঈশ্বরে তার। বিশ্বাস নেই। রোনাটার ছিল, ওর বাবার ছিল। তারা সুখী। রোনাটা বলেছিল যিসাস একদিন ওকে মেষশাবকের মতো বুকে টেনে নেবেন। যত সব বুজরুকি। যিসাস কে? দু-হাজার বছর আগেকার একটা বদ্ধ পাগল। পাগলামির ফলও পেয়েছে। ঝুলতে হয়েছে ক্র থেকে। তার চেয়ে অনেক কাজের লোক প্রমিথিউস, জিয়ুসের কজা থেকে সে আগুনটাকে চুরি করে এনেছিল। অবশ্য শেষরক্ষা হয়নি। ধরা পড়েছিল সেই। ঈগলে টেনে ছিঁড়ে ফেলেছিল তার নাড়িভুড়ি। দূর! এসব কী আবোলতাবল ভাবছে সে পাগলের মতো? পাগলের মতো। সে কি তবে পাগল হতে বসেছে?
***
-আমি নিশ্চিতভাবে জানি, প্রফেসর কার্ল আপনাকে রোনাটার শেষ পত্রখানা দেখিয়েছেন। কী ছিল তাতে? বিশ্বাসঘাতক কে? কীসের? কেন?
-বলব না! বলব না! বলব না! এবং বেশ করব বলব না।
***
কেন বলবে? সে যে নিদারুণ লজ্জার কথা। তার, রোনাটার আর প্রফেসর কার্ল-এর। কী নির্লজ্জ অশ্লীলভাষায় খোলাখুলি লিখেছিল রোনাটা ওই চিঠিখানা। যেন বটতলার উপন্যাস লিখেছে। বের হলেই হু হু করে বিক্রি। কিন্তু রোনাটাকে যে সেই কৈফিয়তটা দেওয়া হয়নি। কেন সে তার প্রথম প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। রোনাটা কি একবার সামনে এসে দাঁড়াতে পারে না? মন উজাড় করে ওকে সব কথা বলে ফেলার একটা সুযোগ দিতে পারে না? আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে–বাস্তবে পরলোক আছে। আত্মা অবিনশ্বর। হয়তো রোনাটা শুনতে পাবে তার কথা।
–আমি নিশ্চিন্তভাবে জানি, আপনি প্রফেসর কার্ল-এর গুপ্তরহস্যটা জেনে ফেলেছেন।
–হ্যাঁ ফেলেছি।
তবে স্বীকার করুন–তিনিই ডেক্সটার।
–আঃ। কী বিড়ম্বনা। তা কেন হবে? হতে পারে তার যমজ ভাই রাশিয়ান গুপ্তচর। তাই তার পিছনে গুপ্ত-আততায়ী ঘুরছে। তার মানে এ নয় যে, তিনিই সেই ডেক্সটার।
-তবে কে? তুমি জান। বল খুলে সব কথা।
–হ্যাঁ জানি। কিন্তু আমি বলব না।
–জান? তুমি জান–ডেক্সটার কে?
–বলছি তো, জানি। তবে বলব না আমি, এবং বেশ করব বলব না।
–বলবে। বলতে তোমাকে হবেই। আমাদের না বলো রোনাটাকে বলে দাও। বি এ ট্রু ক্রিশ্চিয়ান। নিজের ক্র নিজেকেই বইতে হবে যে তোমাকে।
***
মধ্যরাত্রে একদিন উন্মাদের মতো এসে হাজির হল ফুকস জেমস আর্নল্ডের অ্যাপার্টমেন্টে। দ্বার খুলে ওকে দেখতে পেয়ে বিন্দুমাত্র বিস্মিত হল না আর্নল্ড। বললে, আসুন, আপনার জন্যই জেগে বসেছিলাম। আমি জানতাম, আপনি আসবেন।
–আপনি জানতেন? জানতেন, আমি আজ রাত্রে আসব?
–আজ রাত্রেই আসবেন তা জানতাম না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে আসবেন তা জানতাম। এতদিনে মনস্থির করেছেন? বলবেন সব কথা খুলে?
-বলব। এখনই—
বলুন তবে।-কাগজ কলম টেনে নেয় আর্নল্ড।
–না, আপনাকে বলব না। বলব রোনাটাকে।
–রোনাটাকে!?–বিহ্বল হয়ে পড়ে আর্নল্ড।
–হ্যাঁ। একটা টেপ-রেকর্ডার বসিয়ে দিন ওই টেবিলটায়। অনেকগুলো বিল রেখে যান। আর হ্যাঁ–এক বোতল হুইস্কি। ফর হেভেনস্ সেক, আমাকে কোনোভাবে ডিসটার্ব করবেন না। বাড়ি ছেড়ে চলে যান। ঘণ্টা দু-তিন পরে ফিরে এসে টেপটা বাজিয়ে শুনবেন।
–অ্যাজ য়ু প্লিজ, স্যার।
আর্নল্ড তৎক্ষণাৎ যন্ত্রটা বসিয়ে দেয় ওর সামনে। হুইস্কির বোতল আর গ্লাসটা রাখে হাতের কাছে। মানবচরিত্র সে ভালোরকমই বোঝে। আন্দাজ করে, এখন এই অর্ধোন্মাদ অবস্থায় ফুকস্ যদি স্বেচ্ছায় সব কথা স্বীকার করে তবেই রহস্যটা পরিষ্কার হবে। রাত পোহালে হয়তো তার মতটাও পালটে যাবে। তখন আর কিছুতেই নাগাল পাওয়া যাবে না তার।
নির্জন ঘরে তার প্রথম-প্রেমের মুখোমুখি বসল ডক্টর ক্লাউস ফুকস্। মাইকটাকে চুম্বন করল। তারপর ফিসফিস করে ডাকল, রোনাটা। রোনাটা।
.
০৮.
আমাদের বংশে কিছু পাগল আছে, জানলে রোনাটা? আমার বাবা হচ্ছেন এক নম্বর পাগল। তাকে তো তুমি ভালো রকমই চেন। তার ধারণা তিনি হচ্ছেন অ্যাটলাস-জগদ্দল এক পৃথিবীর ভার বহন করতেই তিনি এসেছেন এ দুনিয়ায়। জিয়ুস বুঝি হুকুম দিয়েছে–ওটা ঘাড়ে করে চুপচাপ বসে থাক। ব্যস। বাবা ডাইনে। তাকান না, বাঁয়ে তাকান না–জগদ্দল পৃথিবী ঘাড়ে করে বসে আছেন সারাটা জীবন। আর এক পাগল ছিল প্রমিথিয়ুস। তাকে তুমি চেন না। তার কথা থাক। এছাড়া আমার ছোটো বোন এবং মা-ও পাগল হয়েছিল। আমি কিন্তু তা-বলে পাগল নই। এ আমার আদৌ পাগলামি নয়। ধীর স্থির মস্তিষ্কে সব কথা তোমাকে জানাতে এসেছি। আমি এটুকু বুঝি–তুমি একা নয়, ওরাও এটা জানবে। তা জানুক। আজ গোটা পৃথিবীটাকে ডেকে এ কথা শোনাতে চাই–আমার কথা, তোমার কথা। ভেবে দেখলাম এ ছাড়া পথ নেই। তোমার ‘ড্যাডি’-কে না হলে ওরা মুক্তি দেবে না। এখনই তো প্রায় অন্তরীণ হয়ে আছেন, দুদিন পরে ওঁকে জেলে পুরবে। ওদের যে ধারণা হয়েছে–তিনিই সেই বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে ঘৃণিত বিশ্বাসঘাতক ডেক্সটার। কথাটা সত্য নয়। বিশ্বাস করো রোনাটা–কথাটা সত্য নয়। ওরা ভুল বোঝে বুঝক–কিন্তু তুমি কেমন করে বিশ্বাস করলে–তোমার ড্যাডি এতবড় পাপকাজটা করবেন?
-কী বললে? তা হলে কে সেই ডেক্সটার? আমি চিনি কি না? হ্যাঁ, আমি চিনি। না–রিচার্ড ফাইনম্যান নন, রবার্ট ওপেনহাইমার নন, প্রফেসর অটো কার্লও নন। ডেক্সটার হচ্ছে সেই হতভাগ্য যার বাহুবন্ধনে তুমি ধরা দিয়েছিলে : ডক্টর এমিল জুলিয়াস ক্লাউস ফুকস্।
-প্লিজ রোনাটা। ও-ভাবে ঘৃণায় মুখ ঘুরিয়ে নিও না। আমার কথাটা শেষ পর্যন্ত শোনো। একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করি, কেমন?
***
-তুমি জান, আমার জন্ম ফ্রাঙ্কফুর্ট-এর কাছাকাছি একটা গ্রাম-রাসেলশীম-এ 1912তে। না, পঁচিশে ডিসেম্বর নয়, তার চারদিন পরে। প্রচণ্ড শীতের রাত্রে। আমরা দুই ভাই, দুই বোন। দাদা গেহার্ড, দিদি ক্রিস্টি, আমি, আর আমার ছোটো বোন লিজা। বাবা ছিলেন পাদরি–প্যাস্টর এমিল ফুকস। খ্রিস্টান ধর্মযাজক হয়েছিলেন অনেক পরে–উনিশ শ পঁচিশে; আমার বয়স তখন বছর তেরো। তার আগে তিনি ছিলেন একটি কারখানার মেশিনম্যান। লেদ আর ওয়েল্ডিং-এর দক্ষ কারিগর। সে-যুগের কথা তুমি জান না। তুমি যখন তাকে দেখেছ তখন তিনি কোয়েকার্স সম্প্রদায়ভুক্ত। বিশ্বভ্রাতৃত্বের পূজারী–সোসাইটি অব ফ্রেন্ড এর একজন কর্ণধার। আমি তাকে মিস্ত্রী হিসাবেও দেখেছি।
একদিনের কথা মনে পড়ছে। তখন আমার বয়স কত হবে? এই ধর ছয়-সাত। আমরা থাকতাম ফ্রাঙ্কফুর্টের কাছাকাছি একটা কারখানার বাড়িতে। দু কামরার একটা ছোট্ট বাড়িতে। সৎ ও দক্ষ কর্মী হিসাবে কারখানায় বাবার খুব সুনাম ছিল। সবাই তাকে খুব শ্রদ্ধা করত। এই সময় আমাদের পাড়ায় এক ভদ্রলোকের কুকুরের বাচ্চা হল। ভারি সুন্দর বাচ্চাগুলো। লোমে ভর্তি। আমি আর লিজা রোজ ওই কুকুরছানাগুলোকে দেখতে যেতাম। ভদ্রলোকের নামটা আজ আর মনে নেই, তবে তার চেহারাটা মনে আছে। আমাদের পাড়ার মনিহারি দোকানের মালিক, মধ্যবয়সী, মোটা, একমাথা টাক। রোজ আমাদের ভাইবোনকে কুকুরের লোভে আসতে দেখে উনি একদিন নিজে থেকেই বললেন, কী খোকা? একটা কুকুরছানা নেবে?
আমি তো লাফিয়ে উঠি? বলি, দেবেন?
–দেব। তবে বিনা-পয়সায় নয়। দাম দিতে হবে। এক মার্ক।
এক মার্ক কতটা তখনও বুঝি না। তবে বামা-মা দুজনেই আমাকে খুব ভালোবাসেন। একটা মার্ক কি আর দেবেন না? আমি নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরে আসি। মাকে বলি, মা একটা মার্ক দেবে? ওই দোকানদার ভদ্রলোক তাহলে আমাকে একটা কুকুরছানা দেবেন বলেছেন।
মা জানতেন, কুকুরছানাটা আমার প্রাণ। তৎক্ষণাৎ এক ডয়েশমার্ক আমার হাতে দিলেন। আবার নাচতে নাচতে আমি ভদ্রলোকের কাছে ফিরে গেলাম। উনি বোধহয় আশা করেননি আমি বাড়ি থেকে একটা ডয়েশমার্ক নিয়ে আসতে পারব। আসলে কুকুরছানাটা হস্তান্তরের কোনো বাসনাই ছিল না তার। শুধু শুধু বাচ্চা পেয়ে আমাকে নাচাচ্ছিলেন। এখন কায়দা করে বললেন, এরকম মার্ক-এ তো হবে না খোকা। দেখছ না, আমার কুকুরের লেজ নেই। ডয়েশমার্কেও ‘টেইল’ থাকলে চলবে না। এমন মার্ক আনতে হবে যার দু-দিকেই হেড অর্থাৎ দুদিকেই কাইজারের মুখ ছাপা।
আমি অভিমান করে বলি, সে কথা আগে বললেই হত।
আবার ফিরে এলাম বাড়িতে। মাকে বলি, এ মার্কে হবে না মা, কুকুরের যে লেজ নেই। দু-মুখে রাজার ছাপওয়ালা মার্ক একটা দাও।
মা তো আমার মতো পাগল নন। বললেন, অমন মার্ক হয় না বাছা। ও-লোকটা তোমাকে কুকুরছানা দেবে না, তাই এমন অদ্ভুত দাবি করছে।
আমি কিছুতেই শুনব না। ক্রমাগত ঘ্যানঘ্যান করতে থাকি। শেষমেশ মা আর মেজাজ ঠিক রাখতে না পেরে এক ঘা মেরেই বসেন আমাকে। অভিমানে আমি সারাদিন জলস্পর্শ করি না। মা অনেক সাধ্যসাধনা করলেন, টাকশালে কীভাবে মুদ্রা ছাপা হয় বোঝাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু আমিও অবুঝ। সারাটা দিন প্রায়োপবেশনেই গেল।
সন্ধ্যার পর বাবা ফিরলেন। প্যাস্টর ফুকস্ নন, লেদম্যান ফুক। মায়ের বিরুদ্ধে আমার এবং আমার বিরুদ্ধে মায়ের অভিযোগ মন দিয়ে শুনলেন। তারপর মাকেই ধমক দিলেন, তা তুমিও তো আচ্ছা বাপু। শুনছ কুকুরটার লেজ নেই। বাক্স খুঁজে দু-দিকে রাজার মুখওয়ালা একটা মার্ক ওকে দিলেই পারতে।
মা রাগ করে বললেন, তুমিও ওকে খেপিয়ে তুলছ! এমনিতে পাগল ছেলেটা সারাদিন খায়নি–
বাবা বাধা দিয়ে বললেন, তুমি থাম দেখি।
তারপর আমাকে বললেন, ঠিক আছে খোকা। কাল তোমাকে আমি অফিস থেকে অমন একটা মার্ক এনে দেব। চল, এবার আমরা খেয়ে নিই।
আমি সোৎসাহে বলি, তোমার অফিসে অমন দুমুখো মার্ক আছে?
–কত।
মা বাবাকে ধমক দেন, কেন নাচাচ্ছ ওকে? কাল আবার এই কাণ্ড হবে।
বাবা বললেন, সে তোমাকে ভাবতে হবে না। যাও, আমাদের দুজনের খাবার নিয়ে এস।
পরদিন সারাটা দিনমান আমি বাবার ফেরার পথ চেয়ে বসে থাকি। সন্ধ্যার পর তিনি ফিরতেই আমি লাফিয়ে উঠি, আমার সেই দু-মুখো মার্ক?
বাবা অন্যমনস্কের মতো পকেট থেকে একটা মার্ক নিয়ে আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। কুড়িয়ে নিয়ে আমি একেবারে লাফিয়ে উঠি। দুদিকেই ‘হেড’, ‘টেইল’ নেই।
তখনই ছুটে বেরিয়ে গেলাম এবং মিনিট পনেরো পর কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এলাম বাড়িতে।
দেখি, ইতিমধ্যে মা বাবার জন্য খাবার বেড়ে দিয়েছেন। বাবা কিন্তু খেতে বসেননি। আলমারি থেকে তাঁর দোনলা বন্দুকটা নিয়ে পরিষ্কার করছেন। আমি ফিরতেই বললেন–কী হল জুলি? কাঁদছিস কেন? কুকুরছানা কই?
আমি চোখ মুছতে মুছতে বলি, দিল না। বললে, এটা অচল মার্ক।
বাবা উঠে দাঁড়ালেন। বন্দুকটাও তুলে নিলেন হাতে। বললেন, আয় দেখি আমার সঙ্গে।
মা পিছন থেকে ডাকেন, কোথায় যাচ্ছ? খেয়ে যাও। ও লোকটা কুকুরছানা দেবে না, বুঝতে পারছ না?
-খাবারটা তুলে রাখ। ফিরে এসে খাব।
আমার বয়স, আগেই বলেছি, তখন ছিল মাত্র ছয় কি সাত। তবু দৃশ্যটা স্পষ্ট দেখতে পাই আজও। বাবা ছিলেন অত্যন্ত শান্ত নম্র স্বভাবের মানুষ। কোনোদিন তাকে রাগতে দেখিনি। অথচ সেদিন তাকে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মতো জ্বলে উঠতে দেখেছিলাম। বাবার সেই রুদ্রমূর্তির সামনে দোকানদার ভদ্রলোক একেবারে কেঁচো। বাবা বললেন, আপনি মানুষ না জানোয়ার মশাই? আমার ছেলেকে কেন। এভাবে মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়েছেন? জবাব দিন?
লোকটা আমতা আমতা করে বলে, কিন্তু এটা যে অচল মার্ক স্যার।
–আমিও তো তাই বলছি। এমন মার্ক হয় না জেনেও তা কেন দাবি করেছিলেন আপনি? আপনি কী চান? জার্মানির সব শিশু বড় হয়ে আপনার মতো জোচ্চোর থোক?
-আমার মতো জোচ্চোর?
–জুয়াচুরি নয়। প্রথমত, অসঙ্গত দাবি, দ্বিতীয়ত, ও তা পূরণ করার পরেও আপনি আপনার প্রতিশ্রুতি রাখেননি। আপনি কুকুরছানাটি একে না দিলে আমি আপনাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবো। ‘পাবলিক’ নুইসেন্স হিসাবে মাজায় দড়ি পরাবো আপনার!
ভদ্রলোক হাত দুটি জোর করে বলেন, স্যার, নিয়ে যান আপনার কুকুরছানা। ওই অচল মার্কে আর আমার প্রয়োজন নেই। আমিই বরং উল্টে আপনাকে পাঁচ মার্ক দিচ্ছি–শুধু বলে যান, অমন একটা দু-মুখো মার্ক কোথা থেকে পয়দা করলেন আপনি?
কুকুরছানা নিয়ে আমরা ফিরে এলাম।
তুমি হয়তো ভাবছো এ-সব প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক কাহিনি কেন শোনাচ্ছি তোমাকে। অসংলগ্ন-গল্প নয়, রোনাটা–এ কাহিনিটাও প্রাসঙ্গিক। আমি যা করেছি তা কেন করেছি বুঝতে হলে তোমাকে জানতে হবে কী ভাবে আমি গড়ে উঠেছি।
সেদিন বুঝিনি, আজ বুঝতে পারি কী পরিশ্রম করে দক্ষ কারিগরটি দুটি মার্ককে মাঝামাঝি মেসিনে চিরে আবার জোড়া দিয়েছিলেন। কেন? তার উদ্দেশ্য ছিল–তার সন্তান যেন জুয়াচুরি না শেখে। ছয় বছরের ছেলের কথার খেলাপ হতে দেবেন না বলে এতটা পরিশ্রম করেছেন। এইভাবেই তিনি আমার চরিত্রটা গঠন করতে চেয়েছিলেন।
***
আমার বয়স যখন তেরো, তখন বাবা কোয়েকার হলেন। বিশ্বভ্রাতৃত্বের পূজারী। চার্চের অনুষ্ঠানভিত্তিক ধর্মের ভড়ং নয়, তিনি যিসাস্-এর ওই একটি বাণীকেই মূলমন্ত্র করলেন–’ল্যভ দাই নেবার। বিশ্বপ্রেম। মানবপ্রেম মন্ত্র হল তার-ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা বিসর্জন দিয়ে। আমাদের বাড়ির আর সবাই রাতারাতি ধার্মিক হয়ে উঠল–কেউ আন্তরিক, কেউ বাবাকে খুশি করতে। একমাত্র ব্যতিক্রম তেরো বছরের একটি কিশোর-প্রহ্লাদকুলে দৈত্য-এই জুলিয়াস ক্লাউস ফুকস্। মনে মনে আমি নিরীশ্বরবাদী ছিলাম। মনে করতাম ধর্ম একটা ভড়ং। বিজ্ঞানচর্চা শুরু করেছি তখন। যার প্রমাণ নেই তা মানি না। বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ দাও ঈশ্বর আছেন, তবেই মানবো, নচেৎ নয়। অবশ্য আমার এ মনোভাব কাউকে কখনও বলিনি। বাবা সেটা টের পেলেন আরও দু বছর পরে, আমার ষোড়শ জন্মদিনে।
জন্মদিনে বাবা আমাকে উপহার দিলেন যিসাস-এর একটা ছবি। ফ্রেমে বাঁধানো। আমার পড়বার টেবিলে সেটা রেখে দিলেন আর নিজে হাতে লিখে দিলেন সুইস বিদ্রোহী-কবি উইলিয়াম টেল এর একটি চার-লাইনের কবিতা :
চিরউন্নত বিদ্রোহী শির লোটাবে না কারও পায়ে।
তোমারেই শুধু করিব প্রণাম, অন্তরতম প্রভু!
জীবনের শেষ শোণিতবিন্দু দিয়ে যাব দেশ-ভাইয়ে
রহিবে বিবেক। সে শুধু আমার। বিকাবো না তারে কভু।
বললেন, জুলি, এটাই আমার জীবনের ব্রত। এই ব্রতে তুমিও দীক্ষা নিও।
আমি জবাব দিইনি।
পরদিন বাবা ঘুম ভেঙে উঠে দেখলেন যিসাসের ছবিখানি তার টেবিলের ওপর রাখা। কারণটা জানতে আমার ঘরে উঠে এলেন–দেখলেন ওই কবিতার দ্বিতীয় লাইনটা আমি মুছে দিয়েছি।
বাবা বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন এর হেতু কী।
আমি কবিতার শেষ পংক্তিটা আবৃত্তি করলাম মাত্র।
বাবা কিন্তু রাগ করেননি। দীর্ঘসময় আমার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন–কিন্তু আমার মত পরিবর্তন করতে পারেননি। বিজ্ঞান যা জানতে পারেনি আমি তা কিছুতেই মানতে পারলাম না।
আমি নিরীশ্বরবাদী হওয়ায় বাবা নিশ্চয় দুঃখিত হয়েছেন, আহত হয়েছেন–কিন্তু জোর-জবরদস্তি করেননি। মেনে নিয়েছেন আমার যুক্তি। তিনি বলতেন, সময় হলেই প্রভু যিশু মেষশাবকের মতো তোমাকে কোলে টেনে নেবেন।
***
লাইপজিগ কলেজে ভর্তি হলাম। ওই সময়েই কার্ল মার্কস্ পড়তে শুরু করি। দাস কাপিটাল এবং এঙ্গেলস-এর ভাষ্য। এতদিনে পথের সন্ধান পেলাম। হাতে পেলাম আমার বাইবেল। আমি কম্যুনিস্ট হলাম। মনে-প্রাণে। কলেজে পার্টি-পলিটিক্সে যোগ দিয়েছি। সক্রিয় অংশ নিয়েছি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য হেরে গেলাম আমরা। ন্যাশনাল সোসালিস্টরা ক্ষমতা দখল করল। অর্থাৎ হিটলারের নাৎসি পার্টি। 1933এ একদিন কিয়েল থেকে ট্রেনে করে বার্লিন যাচ্ছি হঠাৎ খবরের কাগজে দেখলাম ওরা রাইখস্ট্যাগে আগুন দিয়েছে। কম্যুনিস্ট ছাত্রদের ধরে ধরে হত্যা করছে। তৎক্ষণাৎ কোটের হাতা থেকে আমি পার্টি-ব্যাজটা খুলে ফেললাম। কলেজে আর গেলাম না। শুরু হল আমার আন্ডারগ্রাউন্ড জীবন। প্রথমে মাসদুয়েক জার্মানিতেই ছিলাম। পালিয়ে পালিয়ে। শুনলাম, আমাদের বাড়িতে নাৎসি ছাত্ররা চড়াও হয়েছিল। হামলা করেছে বাবার ওপর। কলেজের হস্টেলেও আমাকে তন্নতন্ন করে খুঁজেছে। ধরা পড়লে ওরা নিশ্চয় আমাকে হত্যা করত। কিন্তু ওরা আমাকে ধরতে পারেনি। সীমান্ত পেরিয়ে চলে গেলাম ফ্রান্সে। পারিতে ছিলাম প্রথমে, তারপর উদ্বাস্তু হিসাবে চলে গেলাম ইংল্যান্ডে।
এর পরের অধ্যায়টা তুমি জান। আশ্রয় পেলাম একটি কোয়েকার্স পরিবারে। ওই পরিবারের একটি মেয়েকে ভালোবেসে ফেললাম। মেয়েটিও আমাকে তীব্রভাবে ভালোবেসে ফেলে। কিন্তু আমি যে তার আগেই আমার জীবনের ব্রত স্থির করে ফেলেছি। বাবা ছিলেন বিশ্বভ্রাতৃত্বের পূজারী, আমি বিশ্ব-সাম্যবাদের। আমার জীবনের লক্ষ্য হল হিটলারকে তাড়িয়ে আমরা, কম্যুনিস্টরা, বার্লিন দখল করব। আমার সে স্বপ্ন আজ সফল হয়েছে, রোনাটা। 1945এর তিরিশে এপ্রিল সেই রাইখস্ট্যাগের ওপর কাস্তে-হাতুড়ি-আঁকা লাল পতাকাটা আমরা উড়িয়েছি।
কিন্তু এ কী জার্মানি ফেরত পেলাম আমরা? বার্লিনের মাঝামাঝি উঠল পাঁচিল। এপারেও জার্মানি ওপারেও জার্মানি–অথচ দুদিকের মানুষ আজ স্বদেশবাসী নয়। তাদের মাঝখানে আজ দুস্তর ব্যবধান।
মন্ত্রগুপ্তি জিনিসটা আছে আমার রক্তে। আমি যে সাম্যবাদের পূজারী তা ঘুণাক্ষরে জানতে পারেনি কেউ, আমি ইংল্যান্ড আসার পর। এখানে আমি ছিলাম ভালো ছেলে। ছাত্রানাম্ অধ্যয়নং তপঃ। দিনে আঠারো ঘন্টা বিজ্ঞান-চর্চা করেছি। সে তুমি দেখেছ। কিন্তু তুমিও জানতে পারনি আমি রাত জেগে রাজনীতির বই পড়তাম। মার্ক-এঙ্গেল-লেনিনের বাণী আমার কণ্ঠস্থ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও ছিল অনেক কম্যুনিস্ট। তাদের সঙ্গে আমি কিন্তু কোনো যোগাযোগ রাখিনি। কারণ আমি লুকিয়ে কাজ করতে চেয়েছিলাম। স্কটল্যান্ডইয়ার্ড তাই সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স দেওয়ার সময় আমার বিরুদ্ধে কিছুই খুঁজে পায়নি। ছিল একটি মাত্র রিপোর্ট। হিটলারের গেস্টাপো-বাহিনি আমাকে ফেরত পাঠাতে বলেছিল প্রাকযুদ্ধ-যুগে। বলেছিল, আমি নাকি কম্যুনিস্ট। স্কটল্যান্ডইয়ার্ড সে রিপোর্টের ওপর কোনো গুরুত্ব আরোপ করেনি কারণ নাৎসিরা তাদের বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে যাচ্ছেতাই মিথ্যা কথা বলতো।
উদ্বাস্তু জীবনের প্রথমেই স্থির করেছিলাম, একলা চলার পথে চলব। তাই চলেছি সারাজীবন। এমন কি যে মেয়েটিকে ভালোবেসেছিলাম তাকেও মন খুলে বলতে পারিনি আমার গোপন কথা। আমার জীবন উৎসর্গীকৃত। যে কোনোদিন আমি ধরা পড়ে যেতে পারি। তৎক্ষণাৎ অবধারিত মৃত্যু। তাই মেয়েটিকে গ্রহণ করতে পারিনি। তাছাড়া আরও একটি বাধা ছিল। সেটাও অনতিক্রম্য। আমরা ছিলাম বিপরীত মেরুর বাসিন্দা। মেয়েটি পরম ঈশ্বরবিশ্বাসী, আমি চরম নাস্তিক। মেয়েটির কাছে ধর্মই ছিল জীবনের নিউক্লিয়াস; আমার জীবনে নিউক্লিয়ার ফিজিক্সই ছিল ধর্ম। তথাকথিত ধর্ম আমার কাছে আফিঙের নেশা। কেমন করে মেলাবো বলো এমন বিপরীত মেরুর বাসিন্দাদের?
অথচ কী আশ্চর্য দেখ! কী অদ্ভুত ঘটনাচক্র। সেই মেয়েটির জীবন জড়িয়ে গেল আমার সঙ্গে নিবিড়ভাবে। আমার জন্যই জীবন দিল সে। আমিও আজ জীবন দিতে বসেছি তার জন্য।
বিশ্বাস কর রোনাটা-তোমার ড্যাডি, প্রফেসর কার্ল, এর সাতে-পাঁচে নেই। তার যমজভাই আজ রাশিয়া থেকে পালিয়ে আসতে চান। কেন চান, তা জানি না। তিনিও প্রফেসর কাপিৎজার সহকর্মী। নিঃসন্দেহে তার কাছ থেকেই প্রফেসর কার্ল কাপিজার শেষ সংবাদটা পেয়েছিলেন, আমার কাছে স্বীকার করেননি। প্রফেসর কার্ল-এর ধারণা এবং আর্নল্ডের দৃঢ় বিশ্বাস–সেদিন তাকেই গুলি করে মারতে চেয়েছিল সেই আততায়ী। হয়তো তাকে হ্যান্স বলে ভুল করেছিল হত্যাকারী। আবার তা নাও হতে পারে। হয়তো আমাকেই মারতে চেয়েছিল সে।
1942এ আমি প্রথম রাশিয়ান গুপ্তচরদের সঙ্গে যোগাযোগ করি। নিজে থেকে। কেমন করে জান? আমি সোজা চলে গিয়েছিলাম লন্ডনের রাশিয়ান এম্বাসিতে। ছদ্মবেশে। তখন আমি ব্রিটিশ অ্যাটমিক রিসার্চে নিযুক্ত। ওরা আমার কথা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিল। এমন গুপ্তচর ওরা কখনও দেখেনি–যে স্বেচ্ছায় খবর দিতে আসে। বিনিময়ে যে অর্থ দাবি করে না। ওরা বললে, এর পর যেন কোনো কারণেই ওদের এম্বাসিতে না আসি। যোগাযোগ রক্ষা করত একটি ছেলে। তার আসল নামটা জানি না। ছদ্মনাম ছিল আলেকজান্ডার*। [* আসল নামটা ক্লাউস ফুকস কোনদিনই জানতে পারেননি। তার নাম ছিল দাভিনোভিচ ক্রেমার। রাশিয়ান। যুদ্ধান্তে সে রাশিয়ায় ফিরে যায়।] নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট স্থানে সে হাজির হত। আমি তার হাতে তুলে দিতাম আমার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলাফল। শুধু আমার নিজে হাতে করা এক্সপেরিমেন্টের কথাই তখন জানাতাম আমি। কারণ আমার বিবেক বলত, ওই গবেষণার ফলাফল আমার নিজস্ব সম্পত্তি। আমার মস্তিষ্ক থেকে যা বার হচ্ছে তার মালিকানা আমার নিজের। ছেলেটি আরও তথ্য জানতে চাইত। আমি জানতাম না। বলতাম, অপরের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলাফলে আমার মালিকানা নেই। জানলেও তা আমি জানাব না:
‘রহিবে বিবেক। সে শুধু আমার। বিকাবো না তারে কভু।‘
এর পরেই একটা আঘাত পেলাম। রাশিয়ান ছোকরার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করলাম। আঘাতটা কী জান? স্তালিন হিটলারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হলেন। অনাক্রমণাত্মক চুক্তি। আমি মরমে মরে গেলাম। স্তালিনকে কোনো দিন মহান নেতা বলে মনে হয়নি আমার। আমি বরং ছিলাম ট্রটস্কির ভক্ত। কিন্তু স্তালিন যখন রাশিয়ার একনায়ক হয়ে পড়লেন তখন বাধ্য হয়ে তাকে মেনে নিলাম। বিশ্বসাম্যের খাতিরে। হিটলারের সঙ্গে যেদিন স্তালিন চুক্তিবদ্ধ হলেন সেইদিনই ওই গুপ্তচরবৃত্তিতে ক্ষান্ত দিলাম। ওই বিবেকের নির্দেশেই।
কিন্তু ওখানে তো শেষ নয়। কালের রথচক্র আবার এক পাক ঘুরল। হিটলার আক্রমণ করে বসল সাম্যবাদের রাজ্য। যে পথ দিয়ে নেপোলিয়ন মৃত্যুর মুখে এগিয়েছিল ঠিক সেই পথ ধরেই এগিয়ে চলল হিটলারের ব্রিসক্রিগ বাহিনী। মস্কো তাদের লক্ষ্য। কম্যুনিজম-এর নাভিশ্বাস উঠেছে তখন। আমার বিবেক আবার পরিষ্কার হয়ে গেল। আমি স্বেচ্ছায় আবার যোগাযোগ করলাম রাশিয়ান গুপ্তচরদের সঙ্গে। সাম্যবাদের এতবড় সর্বনাশ দেখে আমি আগের চেয়েও এক পা এগিয়ে গেলাম। যেসব আবিষ্কার আমার নয় তাও জানাতে শুরু করলাম ওদের।
এর পরের পর্যায় মার্কিন মুলুকে। স্যার জন কক্ৰট, চ্যাডউইক, প্রফেসর কার্ল প্রভৃতির সঙ্গে আমারও যাওয়ার কথা উঠল। আবার সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স প্রয়োজন হল। আবার তদন্ত হল। কিছুই পাওয়া গেল না–একমাত্র সেই নাৎসিদের ‘মিথ্যা’ দোষারোপখানা ছাড়া। ভাগ্যে ওদের মিথ্যাবাদী বলে বদনাম ছিল। চলে গেলাম আমেরিকায়। প্রথমে শিকাগো, পরে লস অ্যালামসে। এ ছাড়াও দু-একটি কেন্দ্রে যেতে হয়েছে আমাকে। লস অ্যালামসে এসে তোমার সাক্ষাৎ পেলাম। তুমি তো অবাক আমাকে দেখে। তার চেয়েও আমি অবাক মিসেস। কার্লকে দেখে। তখনও আমি জানতাম না প্রফেসর অটো কার্ল তোমার ‘ড্যাডি’, অ্যালিসের তুমি আন্টিও নও আসলে।
***
এর পরের ইতিহাস তোমার জানা। যেটুকু জান না তা এই :
আমার দুই বোন ছিল মনে আছে? ছোটো বোন লিজা আত্মহত্যা করে। সে ছিল আর্টিস্ট। ভারি সুন্দর ছবি আঁকত সে-ওয়াটার কালার, অয়েল এবং প্যাস্টেলে। বিয়ে করেছিল একজন রাশিয়ানকে–প্রাণচঞ্চল ফুর্তিবাজ কিটোস্কিকে। হঠাৎ নাৎসিদের হাতে সে ধরা পড়ে। লিজার সহায়তায় বন্দী শিবির। থেকে শেষ পর্যন্ত কিটোস্কি পলিয়ে যায়। সীমান্ত পার হয়ে চলে যায়–চেকোস্লোভাকিয়ায়। এবার নাৎসিরা অত্যাচার শুরু করল লিজার ওপর। লিজা তখন সদ্য-জননী। ওর কোলে তার প্রথম সন্তান রবার্ট–অর্থাৎ বব। মাত্র একমাসের শিশু। তার শরীর খুব দুর্বল। উপায়ান্তরবিহীন হয়ে সদ্যোজাত শিশুকে নিয়ে সে বাবার ওখানে পালিয়ে আসতে চাইল।
এই সময় আর একজন কমরেড এসে লিজাকে জানিয়ে গেল প্রাগে কিটোস্কি ধরা পড়েছে। তাকে নাকি নাৎসিরা নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। প্রথমে চোখ উপড়ে নিয়েছিল, তারপর এক-একটি করে তার সব দাঁত তুলে ফেলে–শেষে গায়ে পেট্রোল ঢেলে দিয়ে আগুন জ্বেলে দেয়। লিজা পাগল হয়ে গেল শুনে। আমাদের বংশে সেই প্রথম পাগল হল। আমি তার আগে দেশ ছেড়েছি। দাদাও নিরুদ্দেশ। দিদি বিয়ে করে আমেরিকায় চলে গেছে। বাবা জেল থেকে সদ্য ছাড়া পেয়েছেন। অগত্যা বাবাকেই যেতে হল–পাগল মেয়েকে বাড়ি ফিরিয়ে আনতে। উন্মাদ মেয়েকে হাত ধরে নিয়ে আসছিলেন বাবা। কী একটা স্টেশনে সে হঠাৎ বাবার হাত ছাড়িয়ে একটা চলন্ত এঞ্জিনের তলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাবার কোলে ছিল বব–এক মাসের শিশু। বাবা কিছু করতে পারলেন না। তার চোখের সামনেই লিজার দেহটা মাংসপিণ্ডে রূপান্তরিত হয়ে গেল।
তুমি হয়তো বলবে : ঈশ্বর করুণাময়।
বাবাও তাই বলতেন।
সবচেয়ে বড় কথা, লিজাকে ভুল খবর দেওয়া হয়েছিল। কিটোস্কি আদৌ ধরা পড়েনি। সে আজও বহাল তবিয়তে জীবিত। রাশিয়ায়। বিয়ে-থা করেছে, ঘর-সংসার করছে। শুনে এবারও বাবা বললেন : ঈশ্বর করুণাময়।
মা কিন্তু তা বললেন না। উল্টে এবার তিনি পাগল হয়ে গেলেন। তবে ঈশ্বর করুণাময় বলেই বোধকরি তাকে বেশিদিন কষ্ট পেতে হয়নি। এবার তিনিও আত্মহত্যা করে বসলেন। ল্যাটা চুকে গেলো।
দাদা নিরুদ্দেশ, আমি পলাতক, ক্রিস্টি আমেরিকায়–তা হোক। গোটা পৃথিবীর বোঝা যখন বইতে পারছেন তখন আর এ শাকের আঁটিটাকে কি আর কাঁধে নিতে পারবেন না? বৃদ্ধ অ্যাটলাস মানুষ করতে থাকেন মা-বাবা-হারা বকে। আমার কৌতূহল হয় জানতে ব-এর পড়ার টেবিলের ওপরও কি বাবা বিশ্বভ্রাতৃত্বের পূজারী উইলিয়াম টেস্-এর সেই চার-লাইনের কবিতাটি উত্তীর্ণ করে দিয়েছিলেন। বও কি মুছে দিয়েছিল দ্বিতীয় লাইনটা?
***
কী কথা যেন বলছিলাম? হ্যাঁ, লস অ্যালামসের কথা। সেখানে মাস ছয়েক কাজ করার পর কদিনের ছুটি নিয়ে আমি চলে গেলাম ম্যাসাচুসেটসে। সেখানে কেমব্রিজে থাকত ক্রিস্টি আর তার স্বামী হেইম্যান। ক্রিস্টিকে আমি আগেই খবর দিয়েছিলাম। এয়ারপোর্টে ওরা আমায় নিতে এসেছিল। এক মার্কিন বন্ধুর গাড়ি নিয়ে। আলাপ হল মার্কিন ভদ্রলোকটির সঙ্গে। বেশ আমুদে লোক। নাম হ্যারি গোল্ড। দিনসাতেক ছিলাম ক্রিস্টিদের বাড়িতে। ওর মধ্যেই একদিন সুযোগ করে হ্যারি নিরিবিলিতে আমাকে বললে, ডক্টর ফুকস্, দীর্ঘদিন তোমার সঙ্গে নিরিবিলিতে দুটো কথা বলব বলে সুযোগ খুঁজছি।
আমি অবাক হয়ে বলি, বল কী হে! তোমার সঙ্গে আলাপই তো হয়েছে আজ পাঁচদিন।
হ্যারি গোল্ড ঝুঁকে আসে আমার কাছে। প্রায় কানে কানে বলে, আই কাম ফ্রম জুলিয়াস।
–আমি জুলিয়াসের কাছ থেকে আসছি।
আমার রক্তের মধ্যে একটা শিহরন খেলে গেল। এটাই ছিল আমাদের সঙ্কেত। ওই কোড-ম্যাসেজ নিয়েই দীর্ঘদিন পূর্বে আলেকজান্ডার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে। কিন্তু সাবধানের মার নেই। হ্যারি গোল্ড আমেরিকান। সে এফ. বি. আই, নিযুক্ত কাউন্টার-এসপায়ওনেজের এজেন্ট হতে পারে। আমি ন্যাকা সেজে বলি, তার মানে?
তার মানে আমার গাড়িতে ওঠো।
নির্জনে এসে সে অকাট্য প্রমাণ দাখিল করল। সে দীর্ঘদিন ধরে আমার পেছন পেছন ঘুরছে। রাশিয়ান গুপ্তচর সংস্থা কে. জি. বি.-র নির্দেশে। আমি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছি। ওরা আমাকে ভোলেনি। ইতিমধ্যে আমি ম্যানহাটান প্রজেক্টের অন্যতম মূল খুঁটি হয়েছি। পারমাণবিক বোমার আকার ও আয়তন আমিই কষে বার করেছি। সেটাও বোধহয় কে. জি. বি. জানে; কিন্তু লস অ্যালামসের সতর্ক প্রহরার ভেতর কিছুতেই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে। পারছিল না। শুধু আমার জন্যই হ্যারি গোল্ড ক্রিস্টিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে অপেক্ষা করে বসে আছে-কবে আমি ওদের ওখানে আসব।
এককথায় রাজি হয়ে গেলাম। স্থির হল, চার মাস পরে সান্তা ফে-তে কাস্টিলো ব্রিজের কাছে আমি গোপন তথ্যটি হস্তান্তরিত করব। হ্যারি নিজে আসবে না। আসবে তার এজেন্ট। তারিখটা স্থির হল 6 অগাস্ট 1945, সময়-সন্ধ্যা ছয়টা দশ। কোড মেসেজ ওই একই : আই কাম ফ্রম জুলিয়াস।
তবু সাবধান হলাম আমি। আমরা দুজনে বসে কথা বলছিলাম একটি নির্জন পাব-হাউসের একান্তে। মদের বিলটা আমি দু-টুকরো করে এক টুকরো পকেটে রাখলাম। হ্যারিকে বললাম-তোমার এজেন্ট যেন এই বাকি আধখানা কাগজ আমাকে দেখায়। তাহলে নিশ্চিত বুঝতে পারব সে তোমার কাছ থেকেই আসছে। যে রিপোর্টখানা আমি তাকে দেব তার দাম বিলিয়ন ডলার। আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হতে চাই।
–কত বড় হবে তোমার রিপোর্ট?
–অত্যন্ত ছোটো। একটি মাইক্রোফিম। থাকবে একটি পলমল সিগারেটের প্যাকেটে। মন দিয়ে শোন : তোমার এজেন্ট যেন অতি অবশ্যই একটা পলমলের ভর্তি সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটার রাখে তার ডান পকেটে। আমি আমার প্যাকেটটা বাড়িয়ে ধরে বলব–দেশলাই আছে? সে আমার হাত থেকে প্যাকেটটা নেবে, নিজের পকেটে ঢোকাবে এবং পরমুহূর্তেই তার প্যাকেট আর লাইটার বার করবে। আমরা দুজনে দুটি সিগারেট ধরাব আর তারপর পরিবর্তিত প্যাকেটটা নিয়ে আমি ফিরে আসব।
চমৎকার পরিকল্পনা। সর্বসমক্ষেই ইচ্ছে করলে লেনদেনটা তাহলে হতে পারবে।
–তাই হওয়া ভালো। যত গোপন করতে যাবে ততই ধরা পড়ার ভয়।
–ঠিক কথা। কিন্তু আর একটা কথা। বিনিময়ে আমরা তোমাকে কী দেব?
–বিনিময়ে? না কিছু দিতে হবে না।
–তা কি হয়? জুলিয়াস সেটাও জানতে চেয়েছে।
জুলিয়াসকে বল–তারা আমাকে খুঁজে বার করেনি, আমি তাদের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। গরজটা তাদের নয়, আমার! ঘুষ আমি চাই না। নেব না।
-ঠিক আছে। জুলিয়াসকে বলব।
চার মাস পরে নির্দিষ্ট স্থানে জিনিসটা পৌঁছে দিলাম আমি। কী অদ্ভুত ঘটনাচক্র দেখো। ওই 6 অগাস্টেই প্রথম অ্যাটম বোমা ফাটানো হল। মদ কিনবার অছিলায় আমি চলে এলাম লস অ্যালামস থেকে সান্তা ফে-তে। মদের আসরে যারা উপস্থিত ছিল, তাদের ‘অ্যালেবাই’ নাকি পাকা, এ. বি. আই.-য়ের ধারণা। মূর্খগুলো ভেবে দেখেনি, ওই মদ কিনতে যে সান্তা ফেতে গিয়েছিল তার ঘণ্টাদুয়েকের মতো অনুপস্থিতিকালের কোনো সাক্ষী নেই।
***
তুমি বিশ্বাসঘাতককে ঘৃণা করো। তাই না রোনাটা? আগে আমার কথা সবটা শোনো। তারপর জানিও আমাকে ঘৃণা কর কি না।
আমি সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় এ-কাজ করেছি। অর্থের লোভে নয়, ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য নয়। তবে কেন? কেন?
আমেরিকা আজ বিধ্বংসী মারণাস্ত্রের একচেটিয়া মালিক। মনোপলি বিজনেস! গর্বে তার মাটিতে পা পড়ে না। ধরাকে সে সরা জ্ঞান করছে। কিন্তু কে তার হাতে তুলে দিল এই সম্পদ? কারা? তাদের কয়জন আমেরিকান?
যে ছয়জন প্রাকযুদ্ধ-যুগে ওই সম্ভাবনাময় প্রথম পাঁচটি দুরূহ সোপান অতিক্রান্ত করেছিলেন তাদের একজনও মার্কিন নন–রাদারফোর্ড, চ্যাডউইক, কুরি-দম্পতি, ফের্মি আর অটো হান! ইংল্যান্ড; জার্মানি; ফ্রান্স; ইতালি; আবার জার্মানি! আমেরিকা কই? তারপর দেখ–ওই পাঁচজনের প্রাথমিক নির্দেশ সম্বল করে যে বৈজ্ঞানিক দল হাতে-কলমে পরমাণু বোমাকে বাস্তবায়িত করলেন তারাও অতলান্তিকের এ পারের মানুষ। নীলস বোহর, হান্স বেথে, জেমস্ ফ্রাঙ্ক, এনরিকো ফের্মি, উরে, ৎজিলাৰ্ড, টেইলার, উইগনার, ফন নয়ম্যান, ক্রিস্টিয়াকৌস্কি, রোবিনভি, ওয়াইস্কফ, চ্যাডউইক, ক্লাউস ফুস্ক ই? মার্কিন নাম কই? লরেন্স, কম্পটন ইত্যাদি মুষ্টিমেয় কজন সাচ্চা বিজ্ঞানী ছাড়া আছেন একমাত্র ‘অ্যাটম-বোমার জনক’ ওই ওপেনহাইমার। তার অবদানের কথা সৌজন্যবোধে আর নাই বললাম।
তাহলে? এ অস্ত্রের ওপর আমেরিকার একচ্ছত্র মালিকানা হল কোন যুক্তিতে? যুক্তি একটাই–ক্যাপিটালিস্টের যুক্তি! আমেরিকা টাকা ঢেলেছে। ক্যাপিটাল জুগিয়েছে। ওইসব বিদেশি বৈজ্ঞানিকরা কারখানা-মজদুর বৈ তো নয়? যুক্তিটা তো এই? আমি এই যুক্তি মানতে পারিনি। তুমি পারছো?
দ্বিতীয়ত। বিশ্বাসঘাতক কে, বা কারা? আমাদের বলা হয়েছিল জার্মান জুজুর ভয়েই এই বোমা বানানো হচ্ছে। আসলে আমাদের প্রতিযোগী ছিল চারজন জার্মান বৈজ্ঞানিক-অটো হান, ওয়াইৎসেকার, ফন লে আর হেইজেনবের্গ। আমরা য়ুরোপখণ্ডের বিদেশি বিজ্ঞানীরা–কর্তৃপক্ষের মুখের কথায় বিশ্বাস করে প্রাণপাত খেটেছি পুরো ছটি বছর। কারখানা থেকে লভ্যাংশ যখন ঘোষিত হল তখন মিলমালিক মজদুরদের মুখে লাথি মেরে গোটা লভ্যাংশটাই পকেটজাত করলেন। অ্যাটম বোমা ফেলা হবে কি হবে না সে বিষয়ে আমাদের আর কথা বলার কোন। অধিকার রইল না। ৎজিলাৰ্ড দোরে দোরে মাথা খুঁড়ে মরেন বৃথাই, ফ্রাঙ্ক-রিপোর্ট এর স্থান হল ছেঁড়া-কাগজের ঝুড়িতে, প্রফেসর নীলস বোহরের মতো বিশ্ববরেণ্য বৈজ্ঞানিককে চার্চিল মুখের ওপর বললে–লোকটা কী বকছে? রাজনীতি না পদার্থবিদ্যার কথা? স্বয়ং আইনস্টাইনের দ্বিতীয় চিঠিটা–যা তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্টকে লিখেছিলেন অ্যাটম বোমা না ফেলার জন্য তাকে ট্রুম্যান কোনো মূল্যই দেননি!!
তৃতীয়ত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস জাপান যদি এশিয়াবাসী না হত, পীতবর্ণের পৃথক জাতি না হত, তাহলে ট্রুম্যানগ্রোভ-ওপি এভাবে পৈশাচিক উল্লাসে উন্মত্ত হত না। আমার বাবা বিশ্বভ্রাতৃত্বের পূজারী–আমি বিশ্বসাম্যবাদের। আমি ওদের ক্ষমা করতে পারি না।
চতুর্থত। ক্লাউস ফুকস্ যে অপরাধে বিশ্বাসঘাতক, সে অপরাধে গোজেঙ্কো কেন বিশ্বাসঘাতক নয়, তা আমাকে বোঝাতে পার? সেও কি গোপন তথ্য শত্রুপক্ষকে ফাঁস করে দেয়নি? অথচ তার তো বিচার হল না? কেন? সে ক্যাপিটালিজম-এর দালাল বলে? এই বোধহয় ওদের আইনের নির্দেশ! হিটলার পরাজিত না হলে–ওই ন্যুরেমবার্গে হয়তো বিচার হত গ্রোভস্ আর ট্রুম্যানের! আইকম্যানের সঙ্গে ওদের তফাত কোথায়?
সবচেয়ে দুঃখ কী জান, রোনাটা? এত করেও কিছু হল না। আমার সাধের। জার্মানি আজ দু টুকরো! বার্লিনের মাঝখান দিয়ে উঠেছে কাঁটাতারের বেড়া। যে স্তালিনের রাশিয়ার জন্য কাণ্ডটা করলাম সেও আজ হিটলার হতে বসেছে। পূর্ব জার্মানি, চেকোস্লোভাকিয়ায় দেখেছি তার স্বরূপ! কাপিৎজা আজ সাইবেরিয়ায় বন্দী!
“এ আমরা কী করলাম! কমরেড! এ তুমি কী করলে!”
***
ওরা বলে–বিংশ শতাব্দীর ‘জুডাস’। বিশ্বাস কর রোনাটা–
আমি জুডাস নই, আমি প্রমিথিউস! প্রমিথিউস কে জান? অ্যাটলাসের ভাই। অ্যাটলাস জগদ্দল বোঝা বইছে নির্বিকারে–কিন্তু প্রমিথিউস হচ্ছে আদিম বিদ্রোহী। স্বর্গাধিপতি ‘জিউস’-এর গোপন গুহা থেকে সে চুরি করে এনেছিল অগ্নিশিখা। যে আগুন আলো দেয়, যে আগুন উত্তাপ দেয়। মানুষের কল্যাণে, পৃথিবীকে প্রথম আলোকিত করেছিল সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ধরা পড়ে যায়। জিউস তাকে পর্বতশৃঙ্গের সঙ্গে শৃঙ্খলিত করে–ঈগল পাখি দিয়ে তার যকৃৎ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাওয়ায়। আমাকে ওরা অবশ্য ধরতে পারেনি, আমি নিজেই ধরা দিলাম। স্বেচ্ছায়।
লিজা পাগল হয়ে গিয়েছিল। মাও পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। বিশ্বাস করো রোনাটা, আমি কিন্তু পাগল হইনি। জানি, এ স্বীকারোক্তির পরিণাম কী? প্রমিথিউসের শেষ পরিণাম! না! কৃতকার্যের জন্য আমি বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নই। যা করেছি সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায় করেছি-সুযোগ পেলে আবার এ কাজ করবো! স্বীকার করছি সম্পূর্ণ অন্য কারণে-অনুশোচনায় নয়!
***
আমার সামনে এখন খোলা আছে দুটি মাত্র পথ। পটাসিয়াম সায়ানাইডের ক্যাপসুল রয়েছে আমার পকেটে। এই রাখলাম টেবিলের ওপর। যারা বিচারের প্রহসন করে আমার যকৃৎ ঈগল দিয়ে খাওয়াবার আদেশ দেবে তারা শুনে রাখুক–অনায়াসে এই মুহূর্তে তাদের হাত এড়িয়ে যেতে পারি আমি। কেন যাচ্ছি না জান? তার দুটি কারণ :
আমি পদার্থবিজ্ঞানী, কেমিস্ট নই। তাই কে. সি. এন.-এর চেয়ে কিলো ভোল্টকে আমি বেশি চিনি। ক্যাপসুলের চেয়ে ইলেকট্রিক চেয়ার। সেটাও আসল কথা নয়–আসল কথা এবার চুপি চুপি বলি : শুধু তোমাকেই বলছি!
ইতিমধ্যে আমার অদ্ভুত একটা পরিবর্তন হয়েছে, জানলে? ডায়ালেকটিকাল মেটেরিয়ালিজম-এ এর ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না। সেটা যে কী, তা এদের বলতে যাওয়া বৃথা। এরা বুঝবে না! তোমার কাছে তো যাচ্ছিই–তোমাকে বলব, বুঝবে তুমি। আর একজন বুঝবেন–তিনি আমার বাবা। সে জন্যই ক্যাপসুলটা আমি মুখে পুরতে পারছি না। আমি নিজের ক্ৰস্ নিজের কাঁধে বইতে চাই যে!
মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা পেয়ে আমি একটি অনুরোধ জানাব। আমার বাবাকে শুধু একবার দেখতে চাই : তাকে একটা অনুরোধ করে যাব : আমার সমাধির ওপর কবি উইলিয়াম টেস্-এর ওই চারটি লাইন কবিতা যেন তিনি উত্তীর্ণ করিয়ে দেন। হ্যাঁ, চারটি লাইনই। প্রথম দুটি সমেত :
চিরউন্নত বিদ্রোহী শির লোটাবে না কারও পায়ে
তোমারেই শুধু করিব প্রণাম, অন্তরতম প্রভু!
জীবনের শেষ শোণিতবিন্দু দিয়ে যাব দেশ-ভাইয়ে
রহিবে বিবেক! সে শুধু আমার! বিকাবো না তারে কভু!
তোমার কাছে যাওয়ার সময় হয়ে এল। লর্ড যিসাস্! এবার তুমি মেষশিশুর মতো আমাকে তোমার বুকে তুলে নাও।
আমেন!
সমাপ্ত
৮. পরিশিষ্ট
পরিশিষ্ট ক
শেষ কথা
কাহিনির সমাপ্তি আছে, ইতিহাস থামতে জানে না। আমি এ কাহিনির যবনিকা টেনেছি 1950-এর তিরিশে জানুয়ারি, যেদিন তথাকথিত “বিশ্বাসঘাতক” ডেক্সটার জবানবন্দি দেন। তারপর চব্বিশবার এই পৃথিবী সূর্যপ্রদক্ষিণ করছে। তাই কথাসাহিত্যের খাতিরে যেখানে থেমেছি তার পরের কথা এবার বলি। যা সেদিন ছিল একান্ত গোপন, তার তথ্য জেনে ফেলেছে অন্তত আধ ডজন দেশ। কে কবে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে সে তথ্যটা এই সঙ্গে লিখে রাখি :
আমেরিকা-16 জুলাই 1945
রাশিয়া–23 সেপ্টেম্বর 1949
ব্রিটেন-15 মার্চ 1957
ফ্রান্স–13 ফেব্রুয়ারি 1960
চিন–16 অক্টোবর 1964
ভারত–18 মে 1974
ডক্টর ফুকস-এর আশঙ্কা কতদূর বাস্তব তার ইতিহাস সকলেরই জানা।
ডক্টর জে. ওপেনহাইমারের বিচারের রায় প্রকাশিত হয়েছিল 1958 সালে। বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া হয়; কিন্তু এ কথাও প্রমাণিত হয় যে তিনি পদমর্যাদা অনুযায়ী আচরণ করেননি। কর্তব্যচ্যুতি, মিথ্যাভাষণ ইত্যাদির অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে সরকারি গোপন তথ্যে তার প্রবেশাধিকার প্রত্যাহৃত হয়। এর পর দীর্ঘ নয় বছর ডক্টর ওপেনহাইমার অন্তেবাসীর জীবন যাপন করেন। প্রমাণিত হয়েছিল, মিস ট্যাটুলক তার প্রাকবিবাহ জীবনে প্রণয়িনী মাত্র–ট্যাটুলকের আত্মহত্যার সঙ্গে গুপ্তচর বৃত্তির কোনো সম্পর্ক নেই। মৃত্যুর পূর্বে ওপেনহাইমারকে ‘এনরিকো ফের্মি অ্যাওয়ার্ড’ পুরস্কার দেওয়া হয়, যার আর্থিক মূল্য পঞ্চাশ হাজার ডলার। তার মৃত্যুর পর প্রফেসর হারকন শেভেলিয়ার একটি আত্মজীবনী লেখেন, যার উল্লেখ গ্রন্থপঞ্জীতে করা হয়েছে।
পারমাণবিক-বোমার অপেক্ষা শক্তিশালী মারণাস্ত্র আমেরিকা ও রাশিয়া পর পর আবিষ্কার করে-যার নাম হাইড্রোজেন বোমা অথবা থার্মোনিউক্লিয়ার বোমা। ডেক্সটারের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকদের সাফল্য অন্তত দেড় থেকে দুবছর এগিয়ে আসে। এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, ওই তথাকথিত বিশ্বাসঘাতকের জন্য পৃথিবীর দুটি বৃহত্তম-শক্তির ক্ষমতার সমতা ত্বরান্বিত হয়েছিল।
***
বাস্তব তথ্য থেকে কোথায় কতদূর বিচ্যুত হয়েছি এবার তা স্বীকার করি :
ডক্টর ক্লাউস ফুকস্ ইংল্যান্ডে এসে যে পরিবারে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেই পরিবারে যে মেয়েটি ছিল তার নাম ‘রোনাটা’ নয়। সৌজন্যের খাতিরে নামটা আমি পরিবর্তন করেছি। অনুরূপভাবে হারওয়েল তিননম্বর চেয়ারে অধিষ্ঠিত ডক্টর ফুকসের ওপরওয়ালার নাম প্রফেসর অটো কার্ল নয়। সেই ওপরওয়ালার নাম প্রফেসর রুডলফ পেল। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ফুকসের কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। প্রফেসর অটো কার্ল-এর নামটি কল্পিত। ফুকস-এর ওপরওয়ালা একজন বৈজ্ঞানিক তার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে এবং ফুকে নিয়ে পারি ও সুইজারল্যান্ডে বেড়াতে এসেছিলেন এ কথা সত্য; কিন্তু পারি হোটেলের অভ্যন্তরে যে-সব ঘটনার কথা বলা হয়েছে তা কল্পনা। বলা বাহুল্য, ওই প্রফেসরের তরুণী ভার্যার নামও ‘রোনাটা’ ছিল না। এছাড়া মানসিক বিপর্যয়ে মূল অপরাধী একদিন হঠাৎ থানায় উপস্থিত হয়ে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে-জবানবন্দি দিতে চান এ কথা সত্য; কিন্তু তিনি একটি টেপ রেকর্ডার যন্ত্রের সামনে বসে নির্জনে স্বর্গগতা বান্ধবীকে উদ্দেশ করে তাঁর বক্তব্য রাখেন–এমন কোনো নজির নেই।
অপরাধীর ধারণা ছিল তাঁর মৃত্যুদণ্ড অবধারিত! সে কথা জেনেই তিনি জবানবন্দি দিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবে তার মৃত্যুদণ্ড হয়নি। বিচারকালে আদালত-কর্তৃক নিযুক্ত অভিযুক্তের কৌঁসুলী যুক্তি দেখান–বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে মৃত্যু সেখানেই প্রযোজ্য যেখানে শত্রুপক্ষকে গোপন সংবাদ সরবরাহ করা হয়। এক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল ইঙ্গ-মার্কিন দলের মিত্রপক্ষ। এই আইনের ফাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায়নি। বিচারক আইনে-নির্দেশিত সর্বোচ্চ শাস্তি দিয়েছিলেন-চোদ্দো বছর সশ্রম কারাদণ্ড। বাস্তবে নয় বছর পরে (1959) তাকে মুক্তি দেওয়া হয়–বিজ্ঞানজগতে তার দানের কথা স্মরণ করে।
সদ্যকারামুক্ত অপরাধী পূর্ব জার্মানিতে চলে যান। সেখানে তার অতিবৃদ্ধ ঈশ্বরবিশ্বাসী। পিতৃদেব তখনও জীবিত ছিলেন। পিতাপুত্রের মিলন হয়েছিল। ওঁর পিতৃদেব সাংবাদিকদের বলেন :
Neither he nor I have ever blamed the British people for his sentence. He endured his fate bravely, with determination and a clear conscience. He said to himself, “If I don’t take this step, the imminent danger to hu manity will never cease.” I can only have greatest respect for the deci sion he took.
13.1.74
পুনশ্চ (1988) : পূর্ব-জার্মানির ড্রেসডেনে ফুকস নিউক্লিয়ার রিসার্চ সেন্টারের কর্ণধার হন। 1979-এ অবসর গ্রহণ করে, 1988-এ তিনি মারা যান। 1960 সালে একজন মার্কিন সাংবাদিকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় তিনি বলেন : আমি যা করেছি তা বিবেকের নির্দেশেই করেছি। অনুরূপ অবস্থায় পড়লে আবার আমি তাই করব!
.
পরিশিষ্ট খ
কৈফিয়তের কৈফিয়ৎ
13.1.74 যে ‘কৈফিয়ৎ’ লিখেছিলাম তা সংশোধনের জন্য পুনরায় কৈফিয়ৎ লিখতে হচ্ছে বলে আমি আনন্দিত। সেদিন যে প্রশ্ন তুলেছিলাম তার জবাব দিয়েছিলেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এ-গ্রন্থ ছাপাখানা থেকে বের হয়ে আসার পূর্বেই।
গত আঠারই মে 1974 সকালে রাজস্থান মরুভূমির ভূগর্ভে, একশ মিটার গভীরে, ভারত পরীক্ষামূলকভাবে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ না হ’ক, আপাতত ষষ্ঠ আসন অধিকার করেছে। বিস্ফোরণের ক্ষমতা দশ থেকে পনের হাজার টন টি.এন.টি.-র সমান। এই বিস্ফোরণের বৈশিষ্ট্য হল–এতে ইমপ্লোশন-ডিভাইজ বা সাদা বাঙলায় ‘অন্তর্বিস্ফোরণ পদ্ধতি কাজে লাগানো হয়েছে। এই সাফল্যের প্রত্যক্ষ নায়ক হচ্ছেন ড. সেথনা, ড. রামান্না এবং ড. অনিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। বলাবাহুল্য, অসংখ্য বিজ্ঞানীর দীর্ঘদিনের অতন্দ্ৰসাধনার ফলশ্রুতি হিসাবেই ঐ শেষ তিনজন এ কাজে নায়কের ভূমিকায় নেমেছিলেন। সেই তালিকায় সবার আগে যে নামটি স্মর্তব্য তিনি হচ্ছেন ভারতীয় পরমাণু কর্মপ্রচেষ্টার জনক স্বৰ্গত ডক্টর হোমি জাহাঙ্গির ভাবা। স্যার দোরাবজী টাটা ট্রাস্টের কাছে তিনি বারোই মার্চ 1944তারিখে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : “খুব বেশি হলেও আজ থেকে দুই দশক পরে ভারতকে আর পরমাণু-বিশারদ খোঁজার জন্য বাইরে তাকাতেও হবে না–এদেশের ছেলেরাই তা পারবে।”
আজ শুনে মনে হচ্ছে কথাটা কোনো বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানীর নয়-ব্যয় কোনো জ্যোতিষ-সম্রাটের। একমাত্র দুঃখ-তিনি এ সাফল্য দেখে যেতে পারলেন না। চব্বিশে জানুয়ারি 1966-তে তিনি অমরলোকে চলে গেছেন। বিমান দুর্ঘটনায়!
ড. বিক্রম সারাভাইও দুর্ঘটনায় মারা গেলেন তার পাঁচবছর পরে।
কিন্তু কাজ এগিয়ে চলল এসব দুর্ঘটনা সত্ত্বেও। যার চূড়ান্ত ফলশ্রুতি–আপা… যা দেখতে পাচ্ছি, ঐ আঠারই মে 1974 তারিখের ঘটনাটা।
এই সঙ্গে স্মরণ করবো অধ্যাপক ডি. এম. বসু-কেও। আজ থেকে চল্লিশ বছর আগে-পরমাণু বোমার জন্মের এক দশক আগে তিনি ঐ শক্তির ব্যবহার নিয়ে মাথা ঘামান। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা তার সঙ্গে কথা বলে এর প্রয়োজনীয়তাটা বোঝেন এবং এ দেশে পারমাণবিক গবেষণার আধুনিকীকরণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক পদক্ষেপের সূচনা করেন।
এটা প্রমাণ হয়েছে যে, ভারতীয় বিজ্ঞানীরা ভূগর্ভস্থ পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম। নিঃসন্দেহে এটা বড় রকমের উত্তরণ। এখন আশা করতে ভরসা পাচ্ছি, আমার ‘প্রনাতি’ নিশ্চয় মোমবাতির আলোয় এ গ্রন্থ পড়বে না।
13.6.74
.
পরিশিষ্ট গ
কালানুক্রমিক ঘটনাপঞ্জী ও নির্দেশিকা
কাহিনির আকর্ষণে আমাকে কখনো আগের কথা পরে ও পরের কথা আগে বলতে হয়েছে। পাঠক-পাঠিকার যাতে কালভ্রান্তি না হয় তাই এই তালিকাটি সাজিয়ে দিলাম।
না. সা.
1896 — রণজেন কর্তৃক ‘এক্স-রে আবিষ্কার
1897 — বেকারেল কর্তৃক ইউরেনিয়ামে রেডিয়েশান আবিষ্কার
1898 — টমসন কর্তৃক ইলেকট্রন আবিষ্কার
1901 — মাক্স প্লাঙ্ক কর্তৃক ‘কোয়ান্টাম থিয়োরি’র প্রথম উল্লেখ
1905 — আইনস্টাইনের ‘স্পেশাল থিওরি অব রিলেটিভিটি’
1910 — প্লাঙ্ক ও বোহর কর্তৃক ঐ থিয়োরির ব্যাখ্যা
1918 — রাদারফোর্ড কর্তৃক ‘প্রোটন’ আবিষ্কার
1932 — চ্যাডউইক ‘নিউট্রনের’ অস্তিত্ব প্রমাণ করেন
1933 — রুজভেল্ট আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হলেন
1933 — হিটলার জার্মানির সর্বময় কর্তা
1933 — মাদাম জোলিও কুরি ও মাইটনারের মতানৈক্য
1934 — এনরিকো ফের্মি কর্তৃক ইউরেনিয়াম-পরমাণু বিদীর্ণ
1934 — নোডাক-দম্পতি ঐ পরীক্ষার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন
1934 — পীতর কাপিজা রাশিয়ায় এসে গৃহবন্দী।
1935 — ৎজিলাৰ্ড বিশ্বের বৈজ্ঞানিকদের বিধ্বংসী বোমার বিরুদ্ধে সাবধান করার চেষ্টা করেন।
1935 — হান্স বেথে আমেরিকায় চলে আসেন।
1938 — বার্লিনে পরমাণু-শক্তির সন্ধানে সম্মেলন
1938 — ফের্মি নোবেল পুরস্কার নিয়ে সোজা আমেরিকায়
22.12.1938 — অটো হান পরমাণু-বিভাজনের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেন।
2.8.1939 — আইনস্টাইন রুজভেল্টকে ঐতিহাসিক পত্র লেখেন
2.9.1939 — দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু
11.9.1939 — বার্লিনে ‘ইউরেনিয়াম-প্রকল্প’ জন্মলাভ করে
27.9.1939 — রুজভেল্টের ঐতিহাসিক আদেশ : ‘পা, দি রিকোয়ার্স অ্যাকশন’
22.6.1941 — সোভিয়েট-জার্মান চুক্তি ভঙ্গ করে জার্মানির রাশিয়া আক্রমণ
7.12.1941 — জাপান কর্তৃক পার্ল হারবার আক্রমণ।
8.12.1941 — অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে আমেরিকার যুদ্ধ ঘোষণা
13.8.1942 — ‘ম্যানহাটান-প্রকল্পের জন্ম
17.9.1942 — গ্রোভস্ ঐ প্রকল্পের সর্বময় কর্তা নিযুক্ত
12.6.1943 — ওপেনহাইমার সানফ্রান্সিস্কোয় মিস্ ট্যাটলকের সঙ্গে সন্দেহজনকভাবে সাক্ষাৎ করেন
20.7.1943 — গ্রোভস্ ওপেনহাইমারকে পাকা নিয়োগপত্র দেন
26.8.1944 — বোহর রুজভেল্টকে অ্যাটম-বোমার ব্যবহার বিষয়ে সতর্ক করেন
15.11.1944 — জেনারেল প্যাটন জার্মানির স্ট্রাসবের্গ দখল করেন
11.4.1945 — রুজভেল্টের মৃত্যু
12.4.1945 — ট্রুম্যান আমেরিকার প্রেসিডেন্ট
25.4.1945 — ট্রুম্যান অ্যাটম-বোমা প্রকল্পের কথা প্রথম শোনেন
ঐ — অ্যাটমিক ইন্টারিম কমিটি গঠন
30.4.1945 — বার্লিনের পতন ও হিটলারের আত্মহত্যা
জুন 1945 — অ্যাটম-বোমা নিক্ষেপের বিরুদ্ধে ‘ফ্রাঙ্ক-রিপোর্ট’ দাখিল
16.7.1945. — ট্রিনিটি টেস্টে প্রথম অ্যাটম-বোমার পরীক্ষা
ঐ — গ্রোভস্ বেতারে ট্রুম্যানকে ঐ সংবাদ জানালেন
17.7.1945 — পটসড্যামে চার্চিলকে গোপনে ঐ সংবাদ জানানো হল
19.7.1945 — পটসড্যামে ট্রুম্যান হোস্ট-হিসাবে ভোজ দিলেন।
21.7.1945 — পটসড্যামে স্তালিন হোস্ট-হিসাবে ভোজ দিলেন।
23.7.1945 — পটসড্যামে চার্চিল হোস্ট-হিসাবে ভোজ দিলেন।
24.7.1945 — পটসড্যামে ট্রুম্যান স্তালিনকে দ্ব্যর্থবোধক ভাষায় অ্যাটম-বোমার ইঙ্গিত দেন।
24.7.1945 — ট্রুম্যান অ্যাটম-বোমা নিক্ষেপের চূড়ান্ত আদেশ দিলেন
26.7.1945 — মিত্রপক্ষ থেকে জাপানকে শেষ চরমপত্র ঘোষণা
26.7.1945 — চার্চিল নির্বাচনে পরাজিত; চার্চিলের পদত্যাগ
6.8.1945 — হিরোশিমায় প্রথম অ্যাটম-বোমার বিস্ফোরণ
9.8.1945 — নাগাসাকিতে দ্বিতীয় বোমার বিস্ফোরণ
11.8.1945 — জাপানের আত্মসমর্পণ ঘোষিত
11.8.1945 — ‘ডেক্সটার’ গোপন নথি ‘রেমন্ড’কে হস্তান্তর করে
6.9.1945 — গোজেঙ্কো কানাডার কাছে আত্মসমর্পণ করে
15.9.1945 — ম্যাকেঞ্জি কিং-এর পত্রে বিশ্বাসঘাতকতার কথা ট্রুম্যান জানতে পারেন
3.3.1946 — ‘অ্যালেক’ ধরা পড়ে
জুন, 1945 — ফুকস্ হারওয়েলে আসেন
23.9.1946 — রাশিয়া কর্তৃক পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণ
27.1.1950 — ‘ডেক্সটার’ আত্মসমর্পণ করে ও জবানবন্দি দেয়
2.9.1950 — পন্টিকার্ভো হেলসিঙ্কি থেকে নিরুদ্দেশ হন
1.11.1952 — আমেরিকা হাইড্রোজেন বোমা (৩০ লক্ষ টন টি. এন. টি.) বিস্ফোরণ ঘটায়
12.4.1954 — ওপেনহাইমারের ঐতিহাসিক বিচার শুরু হয়
15.3.1957 — ব্রিটেন কর্তৃক পরমাণু-বোমার পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত
13.2.1960 — ফ্রান্স কর্তৃক পরমাণু-বোমার পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত।
16.10.1964 — কম্যুনিস্ট-চিন কর্তৃক পরমাণু-বোমার পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত
8.5.1974 — ভারত কর্তৃক পরমাণু-বোমার পরীক্ষা সাফল্যমণ্ডিত
13.5.1988 দীর্ঘ চব্বিশ বছর পর প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী পরপর পাঁচটি অ্যাটম বোমা পোখরানের ভূগর্ভে বিস্ফোরণ করান।
15.5.1998 — অ্যাটম বোমা ব্যবহারের ক্ষমতাশালী হিসাবে ভারত ষষ্ঠ রাষ্ট্র বলে স্বীকৃতি পেল।
.
পরিশিষ্ট ঘ
বিদেশী নামের সূচি
[বিদেশী স্থান ও ব্যক্তির নাম বাংলা বানানে আমি যেভাবে লিখেছি, স্বদেশে তা হয়তো সর্বক্ষেত্রে সেভাবে উচ্চারিত হয় না। এজন্য এই তালিকায় রোমান হরফে ঐ বিশেষ্য পদগুলিকে সনাক্ত করা গেল। তারকা-চিহ্নিত বিজ্ঞানী নোবেল-পুরস্কার প্রাপ্ত।]
(1) Alamogordo অ্যালামোগোর্ডো
(2) Alsos অ্যালসস
(3) Amold, Henry হেনরি আর্নল্ড
(4) * Becquerel বেকারেল
(5) * Bethe, Hans হান্স বেথে
(6) * Bohr, Niels নীলস বোহর
(7) Boltzmann বোলৎসম্যান।
(8) * Bom, Max ম্যাক্স বর্ন
(9) Bush, Vaniver ভ্যানিভার বুশ
(10) Bruhat ব্রুহাট
(11) Cario, G ক্যারিও
(12) * Chadwick, James জেমস্ চ্যাডউইক
(13) Chevalier, H হাকন শেভেলিয়ার
(14) Cherwell চেরওয়েল
(15) * Cockcroft, Sir J কক্ক্রফট
(16) * Compton, Arthur আর্থার কম্পটন।
(17) Conant, J জেমস্ কনান্ট
(18) Conel, A J কনেল
(19) * Curie, Irine আইরিন কুরি
(20) * Curie, Joliot জোলিও কুরি
(21) * Curie, Pierre পিয়ের কুরি
(22) * Curie, Marie মেরি কুরি
(23) Dalber ডালবার
(24) Dalhem ডালহেম
(25) Democritus ডেমোক্রিটাস
(26) * Dirac, Paul ডিরাক
(27) * Einstein, A আইনস্টাইন
(28) Eltenton এলটেনটন
(29) Enola Gay এনোলা গে
(30) * Fermi, E এনরিকো ফের্মি
(31) * Feynman, R ফাইনম্যান
(32) * Franck, J জেমস ফ্রাঙ্ক
(33) Frisch, O ফ্রিশ
(34) Fuchs, K ক্লাউস ফুকস
(35) Fulton ফালটন
(36) Gamow, G জর্জ গ্যামো
(37) Gauss, K কার্ল গাউস
(38) Geiger, H হান্স গাইগার
(39) Goetingen, University গোটিনজেন বিশ্ববিদ্যালয়
(40) Goudsmit, S গাউডসমিট
(41) Gouzenko, J গোজেঙ্কো
(42) Groves, L লেসলি গ্রোভস
(43) * Hahn, O অটো হান
(44) Halban হালবান
(45) Hallweck হলওয়েক
(46) Harwell হারওয়েল
(47) * Heisenberg হেইসেনবের্গ
(48) Helmholtz হেল্মহোল্টজ
(49) Hilbert, D ডেভিড হিলবার্ট
(50) Hooper, Admiral অ্যাডমিরাল হুপার
(51) Houtermann হোটেনম্যান
(52) Kapitza, Pyotr পীতর কাপিৎজা
(53) Kistiakovosky কিস্টিয়াকোউস্কি
(54) Klein, F ক্লীন
(55) Lansdale, Col. ল্যান্সডেল
(56) * Laue Max, V ফন ম্যাক্স লে
(57) * Lawrence, E লরেন্স
(58) Lomanitz লোম্যানিটৎজ
(59) Manhattan মানহাটান
(60) Maxwell ম্যাক্সওয়েল
(61) Mckilvi ম্যাককিলভি
(62) Meitner মাইটনার।
(63) * Nerst, W ওয়াল্টার নের্স্ট
(64) Neumann, J V ফন নয়ম্যান
(65) Nichols, Col. নিকলস
(66) Nishina, Y নিশিনা
(67) Noddack. J & W নোডাক
(68) Nordblom নর্ডব্লম
(69) Nun May, A অ্যালেন মে
(70) Oppenheimer, J ওপেনহাইমার
(71) Push, Col. কর্নেল প্যাশ
(72) * Planck, Max ম্যাক্স প্লাঙ্ক
(73) Pontecarvo, Bruno ব্রুনো পন্টিকার্ভো।
(74) Quakers কোয়েকার্স
(75) Rabinowitch, E রোবিনোভিচ
(76) * Roentgen, W রনৎজেন
(77) * Rutherford, Earnest রাদারফোর্ড
(78) Santa Fe সান্তা ফে
(79) Sachs, A সাকস
(80) Skardon. W স্কার্ডন
(81) Sommerfeld সমারফেল্ড
(82) Stimson, H হেনরি স্টিমসন
(83) Strassmann স্ট্রাসম্যান
(84) Szilard, L লিও ৎজিলার্ড
(85) Tatlock. J মিস ট্যাটলক
(86) Teller, E টেলার
(87) * Thomson, J J টমসন
(88) Trinity ট্রিনিটি
(89) * Urey, H ইউরে
(90) Watson, Pa পা ওয়াটসন
(91) Weesberg উইসবের্গ
(92) Weisskopi ওয়াইসকফ
(93) Weizsaeher ওয়াইৎসেকার
(94) * Wigner, E উইগনার
(95) Yalta ইয়ালটা
.
পরিশিষ্ট ঙ
গ্রন্থপঞ্জী
1. Alsop, J&S — We Accuse
2. Armine, M — The Great Decisions : The Secret History of the Atomic Bombs
3. Armine, A — Secret
4. Bertin, L — Atom Harvest
5. Boskin. J, & Kristy. F — The Oppenheimer Affair
6. Bardley, D — No Place to Hide
7. Chevalier, H — L’Homme que roulati etre Dieu [The Man Who wanted To Be God]
8. D’abro, A — The Rise of New Physics
9. Einstein, A — The Evolution of Physics
10. Fermi, E — Atoms in the Family
11. Fuchs, E Pastor — Christ in Catastrophe
12. Gamow, G — Atomic Energy in Cosmic & Human Life
13. Gourdsmit, S — Alsos
14. Grouff, S — Manhattan Project
15. Harrison, J A — The Story of Atom
16. Hoover. EJ — The Crime of the Century (Reader’s Digest, June 51)
17. Irvine, Y — The German Atom Bomb
18. Jungk, R — Brighter Than A Thousand Suns
19. Moorehead, A — The Traitors
20. Robinovitch, I– Minutes to Midnight
21. Rouze, M — Robert Oppenheimer, the Man
22. Do — F. Joliot-Curie
23. Rozenta, S — Niels Bohr, His Life & Works
24. Smythe, HD — Atomic Energy
25. U. S. Govt. Publcn. — On the Matter of J. Oppenheimer -transcript of hearing.
.
পরিশিষ্ট চ
আইনস্টাইনের ঐতিহাসিক চিঠি—
প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে–জার্মান পারমাণবিক বোমার সাবধানবাণী
Letter from Albert Einstein to President Franklin Delano Roosevelt about the possible construction of nuclear bombs.
Old Grove Rd., Nassau Point
Peconic, Long Island
August 2nd, 1939
F.D. Roosevelt
President of the United States
White House
Washington, D.C.
Sir;
Some recent work by E. Fermi and L. Szilard, which has been communicated to me in manuscript, leads me to expect that the element uranium may be turned into a new and important source of energy in the immediate future. Certain aspects of the situation which has arisen seem to call for watchfulness and, if necessary, quick action on the part of the administration. I believe therefore that it is my duty to bring to your attention the following facts and recommendations:
In the course of the last four months in has been made probable through the work of Joliot in France as well as Fermi and Szilard in America–that it may become possible to set up a nuclear chain reaction in a large mass of uranium, by which vast amounts of power and large quantities of new radium like elements would be generated. Now it appears almost certain that this could be achieved in the immediate future.
This new phenomenon would also lead to the construction of bombs, and it is conceivable-though much less certain that extremely powerful bombs of a new type may thus be constructed. A single bomb of this type, carried by boat and exploded in a port, might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory. However, such bombs might very well prove to be too heavy for transportation by air.
The United States has only very poor (illegible) of uranium in moderate quantities. There is some good ore in Candada and the former Czechoslovakia, while the most important source of Uranium is Belgian Congo.
In view of this situation you may think it desirable to have some permanent contact maintained between the Administration and the goup of physicists working on chain reactions in America. One possible way of achieving this might be for you to entrust with this task a person who has your confidence and who could perhaps serve in a unofficial capacity. His task might comprise the following;
a) To approach Government Departments, keep them informed of the further development, and out forward recommendations for Government action, giving particular attention to the problem of uranium ore for the United States;
b) To speed up the experimental work, which is at present being carried on within the limits of the budgers of University laboratories, by providing funds, if such funds be required, through his contacts with private persons who are willing to make a contribution for this cause, and perhaps also by obtaining the co-operation of industrial laboratories which have the necessary equipment.
I understand that Germany has actually stopped the sale of uranium from teh Czechoslovakian mines, which she has taken over. That she sould have taken such early action might perhaps be understood on the ground that the son of the German Under-Secretary of State, Von Weishlicker (sic), is attached to the Kaiser Wilheim Institure in Berlin where some of the American work on uranium is now being repeated.
Yours very truly,
(Albert Einstein)
[ পারমাণবিক বোমা প্রস্তুতের সম্ভাবনা প্রসঙ্গে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্টের কাছে আলবার্ট আইনস্টাইনের চিঠি ]
ওল্ড গ্রোভস রোড,
নাসা পয়েন্ট পিকোনিক,
লং আইল্যান্ড
অগাস্ট ২, ১৯৩১
এফ. ডি. রুজভেল্ট
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট
হোয়াইট হাউস,
ওয়াশিংটন, ডি সি,
মহাশয়,
ই. ফার্মি এবং এল, শিলার্ডের কিছু সাম্প্রতিক কাজের পাণ্ডুলিপি আমার কাছে পাঠানো হয়েছে। সেগুলো দেখে আমার মনে হয়েছে, ইউরেনিয়ম নামক মৌলটি অদূর ভবিষ্যতে শক্তির নতুন এক গুরুত্বপূর্ণ উৎস রূপে ব্যবহৃত হবে। পরিস্থিতির এমন নির্দিষ্ট কিছু পরিবর্তন হয়েছে, যেগুলো আমাদের নজরদারি এবং প্রয়োজনে প্রশাসনের দ্রুত কার্যকর হস্তক্ষেপ দাবি করছে।
গত চার মাস ধরে ফ্রান্সের জোলিও (Jolit) এবং আমেরিকার ফার্মি আর শিলার্ড তাদের কাজের মাধ্যমে দেখিয়েছেন বৃহৎ ভরবিশিষ্ট ইউরেনিয়ামের পারমাণবিক শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়া ঘটানো সম্ভব, এবং এতদ্বারা বিশাল পরিমাণ শক্তি (পাওয়ার) এবং প্রচুর পরিমাণে নতুন ‘রেডিয়ম মৌল বেরিয়ে আসবে। প্রায় নিশ্চিত ভাবেই অদুর ভবিষ্যতেই এটা অর্জিত হতে বাধ্য।
এই যে নতুন-ঘটনা, বোমা প্রস্তুতের দিকে ইঙ্গিত করছে, এবং প্রায় কোনো রকম অনিশ্চয়তার প্রশ্নই থাকছে না, আমাদের বুঝে নিতে আদৌ অসুবিধা হচ্ছে না, এই বোমা হবে নতুন ধরনের অত্যন্ত শক্তিশালী। একটি বোমা যদি জাহাজে করে নিয়ে গিয়ে কোনো বন্দরে বিস্ফোরণ ঘটানো যায়, তাহলে সেই বন্দর তো নিশ্চিহ্ন হবে যাবেই, তার সঙ্গে আশপাশের বেশ কিছু অঞ্চলও ধ্বংস হবে। তবে মনে হচ্ছে এই ধরনের বোমা উড়োজাহাজে বয়ে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে হয়তো বেশি ভারী হবে।
যুক্তরাষ্ট্রে মধ্যম পরিমাণের খুবই কম ইউরেনিয়াম আছে। কানাডা এবং সাবেক চেকোস্লোভেকিয়াতে উৎকৃষ্ট ইউরেনিয়মের খনি আছে।
অন্যদিকে ইউরেনিয়মের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ উৎস হল বেলজিয়ম কঙ্গো।
এই পরিস্থিতিতে আপনি হয়তো বা ভাবতে পারেন, প্রশাসন এবং আমেরিকাতে শৃঙ্খল-প্রতিক্রিয়া (চেইন রি-অ্যাকশন) নিয়ে কাজ করছেন ভৌত-বিজ্ঞানীদের যে-দলটি তাদের মধ্যে একটা স্থায়ী যোগাযোগ রাখা উচিত। এই কাজ করার একটা সম্ভাব্য রাস্তা হল, আপনার আস্থাভাজন এমন একজন ব্যক্তির উপর দায়িত্ব দেওয়া যিনি বেসরকারিভাবে ক্ষমতাবলে কাজটি করবেন।
তার কাজের মধ্যে থাকতে পারে :
(ক) সরকারি বিভাগগুলোর কাছে যাবার জন্য, তাদের অনবরত কাজের অগ্রগতির রিপোর্ট সম্পর্কে অবহিত করা এবং সরকারের করণীয় পদক্ষেপের ব্যাপারে সুপারিশ করা। যুক্তরাষ্ট্রের ইউরেনিয়াম খনির সমস্যাগুলোর দিকে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট নজর দেওয়া।
(খ) পরীক্ষামূলক কাজগুলো ত্বরান্বিত করার জন্য বর্তমান বাজেটের সীমার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারগুলোকে এ ব্যাপারে অর্থ বরাদ্দ করা, প্রয়োজনে এই ধরনের বরাদ্দ কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তার মাধ্যমে এই কাজ করতে চান সেটা সংগ্রহ করা, এবং যে সমস্ত শিল্পে এই কাজের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আছে তাদের সহযোগিতা নেওয়া;
আমি জানতে পেরেছি জার্মানি ইতিমধ্যেই তার দখল করা চেকোস্লোভেকিয়ার ইউরেনিয়ম খনিগুলো থেকে ইউরেনিয়ম বিক্রি বন্ধ করে দিয়েছে। জার্মান আন্ডার সেক্রেটারি অব স্টেটস-এর সন্তান ফন ওয়েসলিশরের বার্লিনের ওয়াইলহেম ইনস্টিটিউট ইউরেনিয়মের ওপর আমেরিকার কাজের পুনারাবৃত্তি চলছে। সেটার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, এই ঘটনা থেকে বোঝা যাচ্ছে তারা খুব দ্রুত এই ধরনের কিছু একটা করতে যাচ্ছে।
আপনার বিশ্বস্ত
অ্যালবার্ট আইনস্টাইন
.
পরিশিষ্ট ছ
আইনস্টাইনের দ্বিতীয় ঐতিহাসিক চিঠি-প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে–আমেরিকান পারমাণবিক বোমার সাবধানবাণী। হিরোশিমা-নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা বর্ষণের 6 ও 9 অগাস্ট 1945) প্রায় সাড়ে চার মাস আগে আইনস্টাইন এই চিঠি লেখেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখনো চলছে–তাই তিনি আগের চিঠির মতো খোলাখুলিভাবে সব কিছু লিখতে পারেননি। তবে চিঠির শেষ প্যারাগ্রাফটির (স্পষ্টাক্ষর আমাদের) ‘formulating policy’ যে বোমা-বর্ষণ নীতি গ্রহণ তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।
25 মার্চ লেখা চিঠিটি হোয়াইট হাউসে পৌঁছয় 12 এপ্রিল–18 দিন পর। তার আগের দিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মারা যান। তার স্থলাভিষিক্ত প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের মানবসভ্যতার প্রতি কর্তব্যবোধের সাবধানবাণী (Iconsider it my duty…’) সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন!!
Letter from Albert Einstein to President Franklin Delano Roosevelt about nuclear physicist Dr. Leo Szilard, 1945
112 Mercer Street
Princeton, New Jersey
March 25, 1945
The Honorable Franklin D. Roosevelt
The President of the United States
The White House
Washington, D.C.
Sir,
I am writing to you to introduce Dr. Leo). Szilard who proposes to submit to you certain considerations and recommendations. Unusual circumstances, which I shall describe further below, induce me to take this action in spite of the fact that I do not know the substance of the considerations and recommendations which Dr. Szilard proposes to submit to you.
In the summer of 1939 Dr. Szilard put before me his views concerning the potential importance of uranium for national defense. He was greatly disturbed by the potensialities involved and anxious that the United States Government be advised to them as soon as possible.
Dr. Szilard, who is one of the discoverers of the neutron emission of uranium on which all present work on uranium is based, described to me a specific system which he devised and which he thought would make it possible to set up chain reactions in unseparated uranium in he immediate future. Having known him for ovedr twenty years, both for his scientific work and personally, I have much confidence in his judgement and it was on the basis of his judgement as well as my own that I took the liberty to approach you in connection with this subject. You responded to my letter dated August 2, 1939 by the appointment of a committee under the chairmanship of Dr. Briggs and thus started the Government’s activity in this field.
The terms of secrecy under which Dr. Szilard is working at present do not permit his to give me information about his work; however, I understand that he now is greatly concerned about the lack of adequate contact between scientists who are doing this work and members of your Cabinet who are responsible for formulating policy. In the circumstances. I consider it my duty to give Dr. Szilard this introduction and I wish to express the hope that you will be able to give his presentation of the case your personal attention.
Very truly your.
(A. Einstein)
[প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্টের নিকট পারমাণবিক বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইনের পত্র ]
১১২, মারসার স্ট্রিট
প্রিন্সটন, নিউজার্সি
মার্চ ২৫, ১৯৪৫
মাননীয় ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট
হোয়াইট হাউস,
ওয়াশিংটন ডি. সি
মহাশয়,
ড. লিও শিলার্ডের সঙ্গে পরিচয় করানোর উদ্দেশ্যেই এই চিঠি, তিনি আপনার নির্দিষ্ট বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য কিছু প্রস্তাব আপনার কাছে পেশ করতে চান। একটা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির (নিম্নবর্ণিত প্যারাগ্রাফে আমি সেটার বিবরণ দিয়েছি) জন্যই আমি এই রকম করছি, যদিও আমি জানি না ড. শিলার্ড আপনার নিকট কী প্রস্তাব পেশ করে আপনার বিবেচনা এবং সমর্থন চান, তার মর্মবস্তুই বা কী আমার জানা নেই।
১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মে ড. শিলার্ড জাতীয় প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে ইউরেনিয়মের সম্ভাব্য গুরুত্ব সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করেন। এই সম্ভাব্যতা তাকে অত্যন্ত বিচলিত করে। তুলেছিল এবং তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে যতশীঘ্র সম্ভব বিষয়টি জানানোর জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন।
ড. শিলার্ড হচ্ছেন এমন কতিপয় আবিষ্কারকদের মধ্যে একজন যারা ইউরেনিয়মের নিউট্রন বিচ্ছুরণ নিয়ে কাজ করছেন এবং সেটার ওপর ভিত্তি করেই আজকের দিনে ইউরেনিয়ম সম্পর্কিত সমস্ত কাজ চলছে। তিনি আমার কাছে তার তৈরি একটা বিশেষ পদ্ধতি-ব্যবস্থা তুলে ধরেন, এবং মনে করেন এর দ্বারা অবিচ্ছিন্ন বা যৌগ ইউরেনিয়ম থেকে অচিরেই চেইন-রিঅ্যাকশন তৈরি করা যাবে। বিগত কুড়ি বছর ধরে তার সঙ্গে পরিচিতির সুবাদে, তার বিজ্ঞান সম্পর্কিত কাজ এবং ব্যক্তিত্ব দু’ দিক থেকেই জানার সুবাদে তার সিদ্ধান্তের প্রতি আমি গভীর আস্থা রাখি। এরই ভিত্তিতে এবং আমার নিজেরও বিবেচনাতে আমি সরাসরি আপনার কাছেই বিষয়টি জানাবার স্বাধীনতাটুকু গ্রহণ করি। আপনি ১৯৩৯ সালের ২ আগস্ট সেই চিঠিতে সাড়া দিয়ে ড. ব্রিগস-এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করেন এবং এতদ্বারা এই ক্ষেত্রে সরকারি কাজকর্ম শুরু হয়।
ড. শিলার্ড বর্তমানে যে ধরনের কাজ করছেন সেখানকার গোপনীয়তা রক্ষার শর্তাবলীর জন্য তিনি তাঁর কাজের বিশদ আমাকে জানাতে পারেন না। যাইহোক, তার কথাবার্তা থেকে আমার মনে হয়েছে, আপনার ক্যাবিনেটের নীতি নির্ধারণ সংস্থা এবং বিজ্ঞানের এই বিশেষ বিষয়ের ওপর যারা কাজ করছেন সেই সমস্ত বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে একটা যোগাযোগের একটা বড় ধরনের ট্র্যাক থেকে যাচ্ছে। এই অবস্থাতে আমার মনে হয়েছে ড. শিলার্ড-কে সরাসরি আপনার সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেওয়া উচিত। এবং আমি নিশ্চিতভাবে আশা ব্যক্ত করতে পারি আপনি তার প্রস্তাবনাতে আপনার নিজস্ব মনসংযোগ দিতে পারবেন।
আপনার বিশ্বস্ত
(এ. আইনস্টাইন)
.
পরিশিষ্ট জ
হিরোশিমা ধ্বংসের সংবাদ জানিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের জয়োল্লাস—
বিশ্বশান্তির এই নাকি প্রথম পদক্ষেপ!!
White House Press Release Announcing the Bombing of Hiroshima, August 6, 1945
THE WHITE HOUSE
Washington, D.C.
STATEMENT BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES
Sixteen hours ago an American airplace dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. It had more that two thousand times the blast power of the British “Grand Slam” which is the largest bomb every yet used in the history of warfare.
The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have been repaid many fold. And the end is not yet. With this bomb we have now added a new and revoluntionary increase in destruction to supplement the growing power of our armed forces. In their present form these bombs are now in production and even more powerful forms are in development.
It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. The force from which the sun draws its power has been loosed against those who brought war to the Far East.
Before 1939, it was the accepted belief of scientists that it was theoretically possible to release atomic energy. But no one knew any practical method of doing it. By 1942, however, we knew that the Germans were working feverishly to find a way to add atomic energy to the other engines of was with which they hoped to enslave the world. But they failed. We may be grateful to Providence that the Germans got the V-l’s and V-2’s late and in limited quantities and even more grateful that did not get the atomic bomb at all.
The battle of the laboratories held fateful risks for us as well as the battles of the air, land, and sea, and we have now won the battle of the laboratories as we have now the other battles.
Beginning in 1940, before Pearl Harbor, scientific knowledge useful in was pooled between the United States and Great Britain, and many priceless helps to our victories have come from that arrangement. Under that general policy the research on the atomic bomb was begun. With American and British scientists working together we entered the race of discovery against the Germans.
The United States had available the large number of scientists of distinction in the many needed areas of knowledge. It has the tremendous industrial and financial resources necessary for the project and they could be deveoted to it without under impairment of other vital was work. In the United States the laboratory work and the production plants, on which a substantial start had already been made, would be out of reach of enemy bombing, while at that time Britain was exposed to constant air attack and was still threatened with the possibility of invasion. For these reasons Prime Minister Churchill and President Roosevelt agreed that it was wise to carry on the project here. We now have two great plants and may lessar works devoted to the production of atomic power. Employment during peak construction numbered 125,000 and over 65,000 individuals are even now engaged in operating the plants. Many have worked there for two and a half years. Few know that they have been producing. They see great quantities of material going in and they see nothing coming out of these plants, for the physical size of the explosive charge is exceedingly amall. We have spent two billion dollars on the greatest scientific gamble in history–and won.
But the greatest marvel is not the size of the enterprise, its secrecy, not its cost, but the achievement of scientific brains in putting together infinitely complex pieces of knowledge held by many men in different fields of science into a workable plan. And hardly less marvelous has been the capacity of industry to design and of labour to operate, the machines and methods to do things never done before so that the brainchild of many minds came forth in physical shape and performed as it was supposed to do. Both science and industry worked under the direction of the United States Army, which achieved a unique success in managing so diverse a problem in the advancement of knowledge in a amazingly short time. It is doubtful if such another combination could be got together in the world. What has been done is the greatest achievenemt of organized science in history. It was done under pressure and without failure.
We are now prepared to obliterate more rapidly and completely every productive enterprise the Japansese have above ground in any city. We shall destory their docks, their factories, and their communications. Let there be no mistake; we shall completely destory Japan’s power to make war.
It was to spare the Japanese people from utter destruction that the ultimatum of July 26 was issued at Potsdam. Their leaders promptly rejected that ultimatum. It they do not now accept our terms they may expect a rain of ruin from the air, the like of which has never been seen on this earth. Behind this air attack will follow sea and land forces in such number that and power as they have not yet seen and with the fighting skill of which they are already well aware.
The Secretary fo War, who has kept in presonal touch with all phases of the project, will immediately make public a statement giving further details.
His statement will give facts concerning the sites at Oak Ridge near Knoxville, Tennessee, and at Richland, near Pasco, Washington, and an installation near Santa Fe, New Mexico. Although the workers at the sites have been making materials to be used producing the greatest destructive force in history they have not themselves been in danger beyon many other occupations, for the utmost care have been taken of their safety.
The fact that we can relese atomic energy ushers in a new era in man’s understanding of nature’s forces. Atomic energy may in the future supplement the power that now comes from coal, oil, and falling water, but at present it cannot be produced on a bases to compete with them. commercially, Before that comes there must be a long period of intensive research. It has never been the habit of the scientists of this country or the policy of this government to withhold from the world scientific knowledge. Normally, therefore, everything about the work atomic energy would be made public.
But under the present circumstances it is not intended to divulge the technical processes to production or all the military applications. Pending further examination of possible methods of protecting us and the rest of the world from the danger of sudden destruction.
I shall recommend that the Congress of the United States consider promptly the establishment of an appropriate commission to control the production and use of atomic power within the United States. I shall give further consideration and make further recommendations to the Congress as to how atomic power can become a powerful and forceful influence towards the maintenance of world peace.
দি হোয়াইট হাউস
ওয়াশিংটন ডি. সি
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বিবৃতি
ষোল ঘন্টা আগে আমাদের বিমান জাপানের হিরোশিমাতে একটা বোমা ফেলে শত্রুর পক্ষে ব্যবহার্য সমস্ত কিছু ধ্বংস করেছে। এই বোমা কুড়ি হাজার টন টি. এন. টির থেকেও বেশি শক্তিশালী। এমনকি আজ পর্যন্ত যুদ্ধ-ইতিহাসে ব্যবহৃত সবচেয়ে শক্তিশালী বোমা ব্রিটিশ ‘গ্র্যান্ড স্লাম’-এর বিস্ফোরণ ক্ষমতার চেয়েও দুই হাজার গুণ বেশি এর বিস্ফোরক ক্ষমতা।
জাপানিরা আকাশ থেকে পার্লহার্বারে এই যুদ্ধ শুরু করেছিল। তাদের আমরা অনেকগুণ বেশি ফেরত দিয়ে দিয়েছি। এখনও এই শোধ চলতে থাকবে না। আমাদের অস্ত্রভাণ্ডারে এই বোমার অন্তর্ভুক্তি আমাদের ক্রমবর্ধমান সশস্ত্র শক্তির ধ্বংস করার ক্ষমতাতে এক বৈপ্লবিক সংযোজন, এখন যেমন-আছে-সেইরকম অবস্থার বোমা তৈরি চালিয়ে যাচ্ছি আমরা এবং ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী বোমা আবিষ্কারের পথে এগুচ্ছি।
এটা একটি পারমাণবিক বোমা। এটি বর্তমান বিশ্বের ক্ষমতার ভারসাম্যে লাগাম টানবে, যে উৎস থেকে সূর্য তার শক্তি আহরণ করে থাকে দূর প্রাচ্যে যারা যুদ্ধ নিয়ে গেছে তাদের ওপর সেই শক্তিকেই যুক্ত করা হয়েছে।
১৯৩৯ সালের পূর্বে বৈজ্ঞানিকরা তত্ত্বগতভাবে বিশ্বাস করতেন পারমাণবিক শক্তিকে মুক্তি সম্ভব। কিন্তু কেউ-ই জানতেন না বাস্তবে এটা কী করে করা সম্ভব। ১৯৪২ সালে আমরা জানতে পারলাম জার্মানরা পারমাণবিক শক্তিকে তাদের যুদ্ধ-যন্ত্রের অন্য এক ইঞ্জিনে ব্যবহার করার জন্য পাগলের মত কাজ করছে এবং তাদের আশা ছিল এর দ্বারাই তারা সমগ্র বিশ্ব-কে পদানত করতে পারবে। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়েছে। আমরা কৃতজ্ঞ যে জার্মানরা V-1, V-2 দেরিতে পেয়েছে এবং তা-ও খুবই সীমিত পরিমাণে। এবং আরও বেশি কৃতজ্ঞ যে তারা পারমাণবিক বোমা বানাতে পারেনি।
স্থল-নৌ-এবং বিমান যুদ্ধের সঙ্গে এই গবেষণা যুদ্ধেও আমাদের নির্ধারক ঝুঁকি ছিল। যাই হোক শেষ পর্যন্ত এই গবেষণা যুদ্ধেও আমরা জয়লাভ করেছি।
১৯৪০ সালে, পার্ল হারবার ঘটার পূর্বে গ্রেট ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং কার্যকারিতা বিষয়ক চুক্তি এবং আমাদের অমূল্য সমস্ত বিজয় শেষ পর্যন্ত পারমাণবিক বোমা তৈরির একটা সাধারণ চুক্তির দিকে নিয়ে যায়। এবং সিদ্ধান্ত হয়। আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেনের বৈজ্ঞানিকরা পারমাণবিক বোমার ওপরে এক সঙ্গে কাজ করবে। আমেরিকার হাতে বিজ্ঞানের নানান শাখা-প্রশাখাতে কাজ করা অনেক দক্ষ-প্রতিভার বৈজ্ঞানিক আছে। আমেরিকার আছে বিশাল শিল্প এবং অর্থনৈতিক ভাণ্ডারের মজুত, যেগুলো কোন রকম অহেতুক জটিলতা ছাড়াই যুদ্ধ-কাজে-ব্যয় করা যেতে পারে। আমেরিকাতে গবেষণার কাজ এবং উৎপাদন-শিল্প যেখানে বেশ ভাল। পরিমাণে উৎপাদন শুরু হয়েছিল, সেগুলো ছিল শত্রুর বিমানহানা যে সমস্ত অঞ্চলে অসম্ভব, সেই রকম অবস্থানে। ঠিক এই সময়ে গ্রেট ব্রিটেন শত্রুর আক্রমণের সামনে পড়ে, সেখানে মুহুর্মুহু জার্মান আক্রমণ চলতে থাকে। এই সময়ে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট এবং প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন যে বোমা তৈরির কাজগুলো এখানেই হবে। এখন আমাদের দুটো বড় প্ল্যান্ট, এবং অনেকগুলো ছোট ছোট শিল্প আছে। যেখানে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের কাজ চলছে। বোমা তৈরির চূড়ান্ত সময়ে নিয়োজিত কর্মী সংখ্যা ছিল ১২৫০০০। এবং এখনও ৬৫০০০ কর্মী প্ল্যান্টগুলো চালু রাখতে কাজ করে চলেছেন। অনেকেই সেখানে দুই কিম্বা আড়াই বছর কাজ করেছে। কেউ কেউ কিছুই বুঝতে পারেন নি। কেউ কেউ জানতেন তারা কিছু উৎপাদনের কাজ করছেন। তারা দেখতেন বিপুল পরিমাণ দ্রব্য প্ল্যান্টের ভেতরে ঢুকছে কিন্তু, কিছুই। বেরুচ্ছে না। কারণ, বিস্ফোরক চার্জগুলোর বস্তুগত আয়তন ছিল খুবই ছোট। বিশ্বের ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক কাজে সব থেকে বড় জুয়া খেলাতে আমরা দুই বিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছি। কিন্তু এই প্রকল্পের চমৎকারিত্ব, এর আকারে, গোপনীয়তায় কিম্বা ব্যয়বহুলতাতে সীমাবদ্ধ নয়, এর আসল চমৎকারিত্ব হল বিশ্বের বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাতে কাজ করা বিভিন্ন মস্তিষ্কগুলোর এক সূত্রে কাজ করে নির্দিষ্ট কার্যকর পরিকল্পনা রূপায়ণ করা। শিল্প সংস্থার পরিকল্পনা তৈরি থেকে চালু করার শ্রমও কম আশ্চর্যের নয়।
এই ধরনের যন্ত্রপাতি এবং পদ্ধতির অতীতে কোন নজির ছিল না, সুতরাং অনেক মনের মস্তিষ্ক-জাত শিল্প একত্রিত হয়ে একটি আকার ধারণ করল। এবং যেমনটি ভাবা। গিয়েছিল সেইরকম ফল-ই ফলল। এক্ষেত্রে বিজ্ঞান এবং শিল্পসংস্থা উভয়েই সরাসরি আমেরিকার সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশে কাজ করেছে। এবং এত ব্যাপক বিভিন্ন। ধরনের সমস্যার মোকাবিলা করে অত্যাশ্চর্য অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের সৈন্যবাহিনী জ্ঞানের জগতে এক বিশাল অগ্রগতি ঘটিয়েছে। আমার মনে হয় না পৃথিবীর অন্য কোথাও এধরনের সমন্বয় সম্ভব! ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সংগঠিত বিজ্ঞানের সাফল্য অর্জন করা গেছে। এবং এটা অর্জিত হয়েছে প্রচণ্ড চাপের মধ্যে এবং অব্যর্থ ভাবে। আমরা এখন প্রস্তুত, আরও দ্রুততার সঙ্গে যে-কোন শহরে জাপানিদের মাটির ওপরে আকাশে ধ্বংস করতে পারি। আমরা তাদের সমস্ত বন্দর ধ্বংস করে ছাড়ব। তাদের সমস্ত শিল্প ধ্বংস করব আমরা! ছিন্ন-ভিন্ন করে দেব তাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা, জাপানের যুদ্ধ করার সমস্ত শক্তি ধ্বংস করব!
জাপানি জনগণকে এই অনিবার্য ধ্বংস থেকে রেহাই দেবার জন্য পোস্টডামে ২৬ জুলাই-এর চরমপত্র দেওয়া হয়েছে। তাদের নেতারা এই চরমপত্র খারিজ করে দিয়েছে। যদি তারা এখনও এই চরমপত্রে দেওয়া আমাদের শর্তাবলী মেনে না নেয়, তাহলে আকাশ থেকে তাদের ওপর ধ্বংসের বর্ষণধারা বর্ষিত হবে। তারজন্য তারা প্রস্তুত থাকুক। পৃথিবী এর আগে এ ধরনের ধ্বংস দেখেনি। শুধু আকাশ থেকেই নয়। এর অনুগামী হবে। আমাদের নৌবহর এবং স্থলবাহিনী! এত বিপুল পরিমাণে এত বিশাল শক্তি নিয়ে তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে যে অতীতে পৃথিবী তা দেখেনি, এর সঙ্গে আছে ইতিমধ্যে প্রমাণিত তাদের লড়াই করার দক্ষতা! যুদ্ধ বিষয়ক সচিব, যিনি এই পরিকল্পনার প্রতিটি স্তরের সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক রেখে চলেছেন, খুব শীঘ্রই জনগণের কাছে এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবৃতি দেবেন। তার বিবৃতিতে নক্সভাইলের সন্নিকটে ওক রিজ এবং পাসকোর কাছে রিচল্যান্ড সাইট সম্পর্কে বিশদভাবে থাকবে। যদিও শ্রমিকরা ইতিহাসের এই সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক শক্তির কিছু বস্তুগত দিকই মাত্র করেছেন। তবুও তাদের নিরাপত্তা অন্যান্য পেশার তুলনায় এমন কিছু বেশি বিপজ্জনক সীমা অতিক্রম করেনি। তাদের নিরাপত্তার জন্য সর্বোচ্চ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
এই যে আমরা পারমাণবিক শক্তিকে মুক্ত করতে পেরেছি, এর ফলে প্রকৃতির অনেক নতুন নতুন ‘বল’ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞানের একটা নতুন যুগের সূচনা হত। বর্তমানে কয়লা, তেল এবং ঝরনার জলই শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ভবিষ্যতে এই পারমাণবিক শক্তিই, তাদের বিকল্প হিসাবে কাজে লাগবে। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত উৎসগুলোর সঙ্গে তুলনা করে এখনই আমরা বাণিজ্যিকভাবে সেটা করতে পারছি না। এটা করার আগে অনেক দিন ধরে দীর্ঘ পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নিবিষ্ট গবেষণার প্রয়োজন।
এই দেশের বৈজ্ঞানিকরা এবং সরকারি নীতি কোন সময়েই বিশ্বের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে অবরুদ্ধ করতে চান না। এটা আমাদের স্বভাব বিরুদ্ধ। সুতরাং পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কে সমস্ত কাজই খোলামেলা জনগণের কাছে তুলে ধরা হবে।
কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রযুক্তিগত সব কিছু খুঁটিনাটি কিম্বা সামরিক প্রযুক্তির সং কিছু প্রকাশ্যে আনা সমীচীন হবে না।
আমি কংগ্রেসের এই সভার কাছে অনুরোধ করছি অনতিবিলম্বে-একটা যথাযোগ্য কমিশন নিয়োগ করে যুক্তরাষ্ট্রে পারমাণবিক শক্তি সম্পর্কিত গবেষণা নিয়ন্ত্রিত করুক। আমি ভবিষ্যতে কংগ্রেসের কাছে এই প্রশ্নে বিবেচনা এবং অনুমোদনের জন্য আমার বক্তব্য রাখব যাতে করে আমাদের দেশ বিশ্বশান্তি রক্ষার শক্তিশালী এবং প্রভাবশালী শক্তি হয়ে ওঠে।
.
পরিশিষ্ট ঝ
হিরোশিমা ধ্বংস করার পরে (আগে নয়!!) জাপানের জনগণের প্রতি যুদ্ধোদ্ধত আমেরিকার সাবধানবাণী!!
Leaflets Dropped On Cities in Japan
Leaflets dropped on cities in Japan warning civilians about the atomic bomb, dropped c. August 6. 1945
TO THE JAPANESE PEOPLE.
America asks that you take immediate heed of what we say on this leaflet.
We are in possession of the most destructive explosive ever devised by man. A single one of our newly developed atomic bombs is actually the equivalent in explosive power to what 2000 of our giant B-29s can carry on a single mission. This awful fact is one for you to ponder and we solemnly assure you it is grimly accurate.
We have just begun to use this weapon against your homeland. If you still have any doubt, make inquiry as to what happened to Hiroshima when just one atomic bomb fell on that city.
Before using this bomb to destory every resource of the military by which they are prolonging this useless war, we ask that you now petition the emperor to end the war. Our president has outlined for you the thirteen consequences of an honorable surrender. We urge that you accept these consequences and being the work of building a new, better and peace-loving Japan.
You should take steps now to cease military resistance. Otherwise, we shall res lutely employ this bomb and all our other superior weapons to promptly and forcefully end the war.
EVACUATE YOUR CITIES.
ATTENTION JAPANESE PEOPLE EVACUATE YOUR CITIES.
Because your military leaders have rejected the thirteen part surrender declaration, two momentous events have occurred in the last few days.
The Soviet Union, because of this rejection on the part of the military has notified your Ambassador Sato that it has declared war on your nation. Thus, all powerful countries of the world are now at war with you.
Also, because of your leaders’ refusal to accept the surrender declaration that would enable Japan to honorably end this useless war, we have employed our atomic bomb.
A single one of our newly dveloped atomic bombs in actually the equivalent in explosive power to what 2000 of our giant B-29s could have carried on a single mission. Radio Tokyo has told you that with the first use of this weapon of total destruction. Hiroshima was virtually destroyed.
Before we use this bomb again and again to destroy every rtsuurce of the milirary by which they are prolonging this useless war, petition the emperor now to end the war. Our president has outlined for you the thirteen consequences of an honorable surrender. We urge that you accept these consequences and being the work of building a new, better, and peace-loving Japana.
Act at once or we shall resolutely employ this bomb and all our other superior weapons to promptly and forcefully end the war.
EVACUATE YOUR CITIES
[ ৬ আগস্টের বোমা বর্ষণ সম্পর্কে সাধারণ নাগরিকদের সতর্ক করে জাপানের বিভিন্ন শহরে বিমান থেকে ফেলা প্রচারপত্র।]
জাপানি জনগণের উদ্দেশে :
আমেরিকা চায় আপনারা এই প্রচারপত্রে যা বলা হয়েছে সেগুলোকে গুরুত্ব দিয়ে মানুন।
আমরা এখন, আজ পর্যন্ত মানুষের তৈরি যতরকম ধ্বংসাত্মক অস্ত্র আছে তার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটির অধিকারী। আমাদের এই নতুন বোমার বিস্ফোরণ ক্ষমতা। একটি অভিযানে দু’ হাজারটি দৈত্যকার B-29 বোমার সমান। এই ভয়াবহ ঘটনা আপনাদের বিবেচনার জন্য রাখা হল। এবং আমরা বিনয়ের সঙ্গে আপনাদের নিশ্চিতভাবে বলছি এটি ভয়ঙ্কর রকমের নির্দিষ্ট লক্ষভেদী।
সবেমাত্র আপনাদের স্বদেশভূমির ওপর আমরা এটার প্রয়োগ শুরু করেছি। এ ব্যাপারে যদি কারুর কোন সন্দেহ থাকে, মাত্র একটা বোমা ফেলার পর হিরোশিমা শহরের কী অবস্থা হয়েছে অনুসন্ধান করে জেনে নিতে পারেন।
সামরিক শক্তির ঘাঁটি এবং উৎসগুলো, যে গুলোর সাহায্যে আপনাদের সরকার এই অহেতুক যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করছে, সেগুলোর ওপর এই বোমা বর্ষণ করার আগেই আমরা চাইছি আপনারা আপনাদের সম্রাটকে অবিলম্বে এই যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য গণ আবেদন করুন! ইতিমধ্যেই আমাদের প্রেসিডেন্ট সম্মানজনক আত্মসমর্পণের তেরো দফা খসড়া প্রস্তাব দিয়েছে। আমরা চাই, আপনারা সেগুলো গ্রহণ করুন এবং নতুন, উন্নততর, শান্তিপ্রিয় জাপান গড়ে তুলুন।
নিজের দেশের সামরিক প্রতিরোধের বিরুদ্ধে আপনাদেরই এগিয়ে এসে পদক্ষেপ নিতে হবে। না হলে আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে এই বোমা সহ আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট সমরাস্ত্র ব্যবহার করে যুদ্ধ থামাতে বাধ্য হব।
শহরগুলো ফাঁকা করে চলে যান
জাপানি জনগণ সতর্ক হোন! শহরগুলো ফাঁকা করে চলে যান!
যেহেতু আপনাদের সামরিক সরকার তেরো দফা আত্মসমর্পণের সনদ অস্বীকার করেছে, দুটো অত্যন্ত বিশাল গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কয়েকদিনের মধ্যেই ঘটে গেল।
আপনাদের সামরিক সরকারের এই অস্বীকার করার ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন আপনাদের রাষ্ট্রদূত স্যাটো-কে দেশ-থেকে তাড়িয়ে দিয়ে আপনাদের জাতির বিরুদ্ধে-যুদ্ধ-ঘোষণা করেছে। এই রকমভাবে সমগ্র বিশ্বের সব কটা শক্তিশালী দেশই আপনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়েছে। আরও, আপনাদের নেতাদের সম্মানজনক ভাবে আত্মসমর্পণের সনদ অস্বীকার করার ফলে এই নিরর্থক যুদ্ধে, আমরা আমাদের পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করেছি।
এর একটা অভিযানে ব্যবহৃত একটা বোমা আমাদের দৈত্যাকার B-29 দু-হাজার বোমার সমান, রেডিও টোকিও আপনাদের জানিয়েছে সর্বাত্মক-ধ্বংসক্ষমতা সম্পন্ন এই বোমার প্রথম প্রয়োগের ফলে হিরোশিমা শহর কার্যত ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।
আমরা চাইছি, যুদ্ধের ঘাঁটি এবং শক্তির উৎসগুলো, যেগুলোর ওপর পুনঃ পুনঃ এই বোমা বর্ষণের আগেই আপনারা আপনাদের সম্রাটকে আমাদের প্রেসিডেন্টের দেওয়া সম্মানজনক আত্মসমর্পণের ১৩ দফা প্রস্তাব নেবার জন্য গণ আবেদন করুন। আপনাদেরও বলছি ওটা মেনে নিয়ে নতুন, আরও ভাল এবং শান্তিপ্রিয় জাপান গড়ে তুলুন।
এখুনিই এটা শুরু করুন! না হলে যুদ্ধ থামানোর জন্য আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে এই বোমা সহ আরও উন্নততর অস্ত্রগুলো ব্যবহার করব। এ যুদ্ধ থামাতেই হবে।
.
Extracts from an U.N. Radio interview, June 16, 1950; recorded in the study of Prof. Einstein’s Princeton, New Jersey, home.
Q. Is it an exaggeration to say that the fate of the world is hanging in the balance?
A. No exaggeration. The fate of human ity is always in the balance…but more truly now than at any known time…
Q. Is it possible to prepare for war and world cominunity at the same time?
A. Striving for peace and preparing for war are incompatible with each other, and in our time more so than ever.
Q. Can we prevent war?
A. There is a very simple answer. If we have the courage to decide our selves for peace, we will have peace…
Q. What is your estimate of the future effect of atomic energy on our civilization in the next ten or twenty years?
A. Not relevant now. The technical possibilities we now have already are satisfactory enough…if the right use would be made of them.
Q. What is your opinion of the profound changes in our living predicted by some scientists…for example, the possibility of our need to work only two hours a day?
A. We are always the same people. There are not really profound changes. It is not so important if we work five hours or two. Our problem is social and economic, at the international level.
Q. United Nations Radio is broadcasting to all the corners of the earth, in twenty-seven languages. Since this is a moment of great danger, what word would you have us broadcast to the peoples of the world?
A. Taken on the whole, I would believe that Gandhi’s views were the most enlightened of all the political men in our time. We should strive to do things in his spirit…not to use violence in fighting for our cause, but by non-participation in what we believe is evil.
অধ্যাপক আইনস্টাইনের প্রিন্সটন আবাসের গবেষণাগারে ইউনাইটেড নেশা এর বেতার সাংবাদিকের সাক্ষাৎকারের অংশবিশেষ [জুন 16, 1950 ]
প্র : যদি বলি পৃথিবীর ভাগ্য আজ একটি সূক্ষ্ম সুতোয় ঝুলছে, তাহলে সেটাকে কি অতিশয়োক্তি বলবেন?
উ : আদৌ নয়। মানুষের ভাগ্য সর্বকালেই অনিশ্চিত..তবে আজকের মতো চরমসঙ্কটের অবস্থা তার কখনো হয়নি।
প্র : আপনি কি মনে করেন যুদ্ধের প্রস্তুতি আর বিশ্ব-সংগঠনের কাজ একযোগে চলতে পারে?
উ : শান্তির প্রয়াস আর যুদ্ধের প্রস্তুতি পরস্পর-বিরোধী প্রচেষ্টা, আজকের দিনে সেটা আরও বেশি সত্য।
প্র : বিশ্বযুদ্ধকে কি আমরা প্রতিহত করতে পারব?
উ : উত্তরটি সহজ ও সরল। যথেষ্ট সাহসিকতার সঙ্গে যদি আমরা কৃতসঙ্কল্প হই, তাহলে বিশ্বশান্তি আমাদের করায়ত্ত হবেই।
প্র : পারমাণবিক শক্তি মানব-সভ্যতায় কী জাতের প্রভাব বিস্তার করবে বলে আপনার ধারণা? ধরুন আগামী দশ-বিশ বছরে?
উ : এখন প্রশ্নটা অপ্রাসঙ্গিক। আমরা আজ পর্যন্ত যে পরিমাণ বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ্যার আশীর্বাদ লাভ করেছি তা পর্যাপ্ত…অবশ্য যদি তা সুপ্রযুক্ত হয়।
প্র : কোনো কোনো বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণী করছেন যে, আমাদের জীবনযাত্রায় প্রভূত পরিবর্তন আসন্ন।…যেমন ধরুন দৈনিক দুই ঘন্টার পরিশ্রমই ভবিষ্যতে যথেষ্ট হয়ে যাবে–এ বিষয়ে আপনার কী অভিমত?
উ : আমরা যা ছিলাম তাই আছি, তাই থাকব। কোনো মৌল পরিবর্তন হয়েছে বলে তো মনে হয় না। দৈনিক কতক্ষণ কাজ করি–দুই না পাঁচ ঘণ্টা-সেটা কোনো বড় কথা নয়। সমস্যাটা সামাজিক এবং অর্থনৈতিক–আন্তর্জাতিক বিচারে।
প্র : ইউনাইটেড নেশা বেতার কর্তৃপক্ষ পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে সাতাশটি ভাষায় প্রচারকার্য চালিয়ে থাকেন। আজ যেহেতু মানবসভ্যতা এক ভয়াবহ সর্বনাশের সম্মুখীন, তাই জানতে চাইছি–বিশ্বমানবকে আপনি আজ কোন্ বাণী শোনাতে চান? উ : সব কিছু বিবেচনা করে আমার মনে হয়েছে, আমার সমকালীন যাবতীয় রাজনৈতিক নেতাদের ভিতর মাত্র একজনের বিশ্লেষণই প্রজ্ঞাদীপ্ত। তিনি হচ্ছেন : গান্ধীজী। তার নৈতিক নির্দেশে পরিচালিত হওয়াই আমাদের কর্তব্য…লক্ষ্যে উপনীত হতে আমরা কিছুতেই হিংসার আশ্রয় নেব না। যা অন্যায়, যা অসত্য তার বিরুদ্ধে অসহযোগ সংগ্রামই হোক আমাদের প্রতিজ্ঞা।

