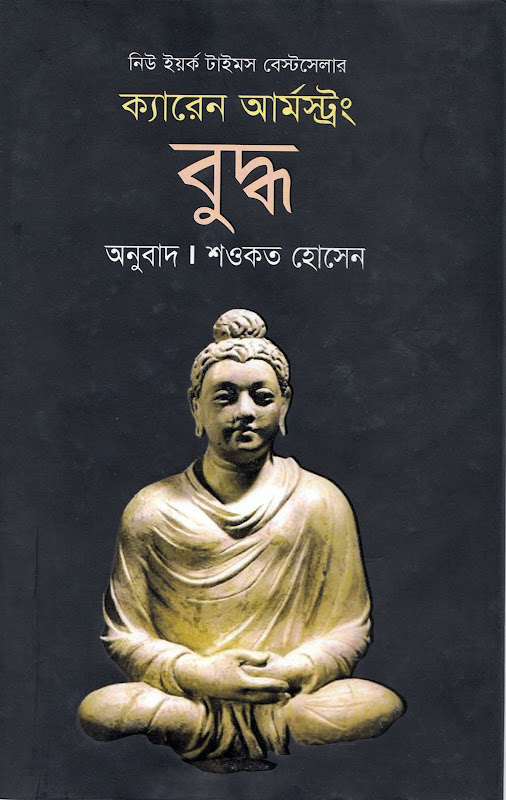- বইয়ের নামঃ বুদ্ধ
- লেখকের নামঃ ক্যারেন আর্মস্ট্রং
- বিভাগসমূহঃ অনুবাদ বই, ইতিহাস, ধর্মীয় বই
বুদ্ধ
০. সূচনা
কোনও কোনও বৌদ্ধ বলতে পারে সিদ্ধার্থ গৌতমের জীবনী রচনা খুবই অবুদ্ধসুলভ ব্যাপার। তাদের চোখে কোনও কর্তৃপক্ষেরই শ্রদ্ধা পাবার যোগ্যতা নেই। বুদ্ধদের অবশ্যই স্বপ্রণোদিত হতে হবে। নির্ভর করতে হবে নিজেদের ওপর, কোনও ক্যারিশম্যাটিক নেতার ওপর নয়। যেমন বৌদ্ধ মতবাদের লিন-চি ধারার প্রতিষ্ঠাতা নবম শতকের এক পণ্ডিত তাঁর শিষ্যদের এমনকি এমন নির্দেশও দিয়েছেন, ‘যদি বুদ্ধের দেখা পাও, বুদ্ধকে হত্যা করো!’ কর্তৃত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হতে স্বাধীন থাকার গুরুত্ব বোঝাতেই এই উক্তি। গৌতম হয়তো এই বাক্যটির সহিংসতা অনুমোদন করতেন না। কিন্তু সারাজীবন তিনিও ব্যক্তির কাল্টের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে গেছেন। অন্তহীনভাবে নিজেকে শিষ্যদের মনোযোগ হতে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। তাই জীবন ও ব্যক্তিত্ব নয়, বরং তাঁর শিক্ষাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বিশ্বাস করতেন অস্তিত্বের গভীরতম কাঠামোয় খোদাই করা সত্যকে জাগিয়ে তুলেছেন তিনি। সেটা হচ্ছে ধম্ম: শব্দটার ব্যাপক দ্যোতনা রয়েছে, তবে প্রাথমিকভাবে দেবতা, মানুষ ও পশুপাখির জীবনের একটা মৌলিক বিধি তুলে ধরে। এই সত্য আবিষ্কারের মাধ্যমে আলোকিত জনে পরিণত হয়েছিলেন তিনি। এক গভীর অন্তর্গত পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করেছেন। জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণার মাঝে শান্তি ও মুক্তি লাভ করেছেন। এইভাবে গৌতম পরিণত হয়েছেন বুদ্ধে–আলোকিত বা জাগ্রতজনে। এই পদ্ধতি অনুসরণ করে তাঁর যেকোনও শিষ্য একইভাবে আলোকিত হতে পারবে। কিন্তু লোকে মানুষ গৌতমকে পূজা শুরু করলে নিজেদের কর্তব্য হতে বিচ্যুত করে বসবে। তখন বিশ্বাস আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়ে মূল্যহীন নির্ভরশীলতার কারণ হয়ে দাঁড়াবে যা কোনও আধ্যাত্মিক অগ্রগতিকেই বাধাগ্রস্ত করবে।
বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থসমূহ এই চেতনার প্রতি বিশ্বস্ত। গৌতমের জীবন ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যেন সামান্যই আমাদের কাছে তুলে ধরে। সুতরাং আধুনিক মানদণ্ড অনুযায়ী বুদ্ধের জীবনী রচনা খুবই কঠিন, কারণ ঐতিহাসিকভাবে সঠিক বিবেচনা করা যাবে এমন খুব সামান্য তথ্যই আছে আমাদের হাতে। ২৬৯ থেকে ২৩২ বিসিই পর্যন্ত উত্তর ভারতীয় সাহরিয় রাজ্য শাসনকারী রাজা অশোকের লিপি থেকে বৌদ্ধ ধর্ম নামে কোনও ধর্মের অস্তিত্বের বিষয়টি প্রথমবারের মতো প্রকাশিত হয়। কিন্তু বুদ্ধের আনুমানিক দুইশো বছর পরের মানুষ ছিলেন তিনি। নির্ভরযোগ্য তথ্যের এই অপ্রতুলতার কারণে ঊনবিংশ শতাব্দীর কোনও কোনও পশ্চিমা পণ্ডিত ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবে গৌতমের অস্তিত্বের ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁদের দাবি ছিল তিনি স্রেফ সেই সময়ের শাক্য দর্শনের ব্যক্তিরূপ বা সৌর কাল্টের কোনও প্রতীক ছিলেন। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতরা এই সন্দিহান অবস্থান থেকে সরে এসেছেন। তাঁরা যুক্তি দেখান, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থসমূহে খুব সামান্য জনপ্রিয়ভাবে পরিচিত ‘গস্পেল সত্যি’ থাকলেও আমরা মোটামুটি নিশ্চিত থাকতে পারি যে সিদ্ধার্থ গৌতমের অস্তিত্ব প্রকৃতই ছিল। শিষ্যরা যতখানি সম্ভব তাঁর জীবন ও শিক্ষার কথা সংরক্ষণ করেছে।
বুদ্ধ সম্পর্কে জানবার প্রয়াস চালাতে গেলে আমাদের বিশাল আকৃতির বুদ্ধ ধর্মগ্রন্থসমূহের ওপর নির্ভর করতে হয়। বিভিন্ন টেক্সটের বিষয়বস্তু জটিল ও এর বিভিন্ন অংশের মর্যাদা বিতর্কিত। তবে এটা মোটামুটিভাবে স্বীকৃত যে, অজ্ঞাত উৎসের উত্তর ভারতীয় পালি ভাষায় লিখিত টেক্সটাই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য। যার সঙ্গে মঘধ ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে হয়। স্বয়ং গৌতম হয়তো এ ভাষায় কথা বলে থাকবেন। থেরাভেদা পদ্ধতির অনুসারী শ্রী লঙ্কা, বার্মা ও থাইল্যান্ডের বুদ্ধরা এইসব গ্রন্থ সংরক্ষণ করেছে। কিন্তু রাজা অশোকের আগে ভারতবর্ষে লেখালেখির খুব একটা চল ছিল না। পালি-বিধান মুখে মুখে সংরক্ষিত হয়েছে এবং সম্ভবত বিসিই প্রথম শতাব্দীর আগে লিপিবদ্ধ হয়নি। কেমন করে এইসব ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়েছিল?
মনে হয় ৪৮৬ সালে (প্রচলিত পাশ্চাত্য সময় অনুযায়ী) বুদ্ধের মৃত্যুর অল্প পরেই তাঁর জীবন ও শিক্ষার কাহিনীগুলো সংরক্ষণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। বুদ্ধ সন্ন্যাসীরা তখন যাযাবর জীবন কাটাতেন। তাঁরা গাঙ্গেয় অববাহিকার শহর-বন্দরে ঘুরে ঘুরে জনগণকে দুঃখ-দুদর্শা থেকে আলোকন ও মুক্তির বার্তা শেখাতেন। অবশ্য বর্ষার সময়ে পথ থেকে সরে যেতে বাধ্য হতেন তাঁরা, নিজেদের বিভিন্ন বসতিতে জমায়েত হতেন তখন। বর্ষাকালীন এই অবকাশের সময়ে সন্ন্যাসীরা তাঁদের মতবাদ ও অনুশীলন নিয়ে আলোচনা করতেন। বুদ্ধের পরলোকগমনের অব্যবহিত পরেই, পালি টেক্সট আমাদের জানাচ্ছে, সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন প্রচলিত মতবাদ ও অনুশীলনের মূল্যায়নের লক্ষ্যে একটা উপায় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সম্মেলন আয়োজন করেন। মনে হয় আনুমানিক পঞ্চাশ বছর পর উত্তর ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় কোনও কোনও সন্ন্যাসী তাঁদের মহান গুরুর কথা মনে রেখেছেন; অন্যরা আরও আনুষ্ঠানিক কায়দায় তাঁদের সাবুদ সংগ্রহ করেন। তখনও এসব লিখতে পারেননি তাঁরা। কিন্তু যোগ অনুশীলন তাঁদের অনেককেই বিস্ময়কর চমৎকার স্মৃতিশক্তি যুগিয়েছিল। তো তাঁরা বুদ্ধের বয়ান ও যার যার গোষ্ঠীর বিধি-বিধানের বিস্তারিত মুখস্থ করার উপায় বের করেছিলেন। যেমনটা স্বয়ং বুদ্ধ হয়তো করে থাকবেন। তাঁরা শিক্ষার একটা অংশকে কবিতায় পরিণত করেছিলেন, হয়তো আবৃত্তি করে থাকবেন (লিখিত টেক্সটে আজও বর্তমান); তাঁরা সূত্রবদ্ধ ও পুনরাবৃত্তিমূল কায়দাও আবিষ্কার করেছিলেন যাতে সন্ন্যাসীরা এইসব বয়ান অন্তর দিয়ে শিক্ষা করতে পারেন। তাঁরা হিতোপদেশ ও বিধিনিষেধকে আলাদা কিন্তু অংশত একইরকম উপাদানের সমগ্রে ভাগ করেছেন এবং বিশেষ সন্ন্যাসীদের এইসব সংকলন মুখস্থ করে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।
বুদ্ধের মৃত্যুর প্রায় একশো বছর পর দ্বিতীয় বারের মতো সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে টেক্সটসমূহ বর্তমান পালি লিপিতে রূপ নিয়েছিল বলে মনে হয়। একে প্রায়শঃই তিপিতাকা (‘তিনটি ঝুড়ি’) নামে অবিহিত করা হয়, কারণ পরবর্তী কালে ধর্মগ্রন্থসমূহ লিপিবদ্ধ করার সময় সেগুলোকে তিনটা ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে রাখা হয়েছিল: বয়ানের ঝুড়ি (সুত্তা পিতাকা), অনুশীলনের ঝুড়ি (বিনয়া পিতাকা) ও বিভিন্ন শিক্ষার একটা মিশ্র রূপ। প্রতিটি ‘ঝুড়ি’ আবার এভাবে ভাগ করা ছিল:
[১] সুত্তা পিতাকা, বুদ্ধের হিতোপদেশের পাঁচটি ‘সংগ্রহে’র (নিকয়া) সমষ্টি :
[ক] দিঘা নিকয়া: সন্ন্যাসীদের আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ, সাধারণ মানুষের দায়িত্ব-কর্তব্য ও বিসিই পঞ্চম শতকের ভারতীয় ধর্মীয় জীবনের নানান বিষয়ের ওপর আলোকপাতকারী দীর্ঘ আলোচনাগুলোর চৌত্রিশটির সংকলন। তবে বুদ্ধের গুণাবলী (সাম্পাসাদানিয়া) এবং তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোর (মহা পরিনিব্বানা) একটি বিবরণও আছে।
[২] মাজহিমা নিকয়া: ১৫২টি মাঝারি দৈর্ঘ্যের হিতোপদেশের (সুত্তা) সংকলন। এগুলোয় রয়েছে বুদ্ধ, আলোকপ্রাপ্তির জন্যে তাঁর সংগ্রাম ও আদি শিক্ষার বিপুল পরিমাণ কাহিনী এবং সেই সঙ্গে মৌল মতবাদের কয়েকটি।
[৩] সাম্যত্তা নিকয়া: অষ্টপথ ও মানুষের ব্যক্তিত্বের গঠনের মতো বিষয় অনুযায়ী বিভক্ত পাঁচটি সুত্তার সিরিজের সংকলন।
[৪] আঙুত্তারা নিকয়া: সুত্তার পাঁচটি ভাগ রয়েছে এখানে যেগুলো ধর্মগ্রন্থের অন্যান্য অংশেও অন্তর্ভুক্ত।
[৫] খুদ্দাকা-নিয়া: ক্ষুদ্র রচনার সংকলন, ধম্মপদের মতো জনপ্রিয় টেক্সট, বুদ্ধের শ্লেষ মেশানো কৌতুক গল্প ও ক্ষুদে কবিতা যার অন্তর্ভুক্ত; উদানা, বেশির ভাগই কাব্যরূপে রচিত বুদ্ধের আপ্ত বাক্যের সংকলন, প্রতিটি কেমন করে আবৃত্তি করতে হবে তার কায়দাসহ সূচনা সম্বলিত; বুদ্ধের জীবন সম্পর্কিত কিছু কিংবদন্তী সম্বলিত কাব্যের আরেকটি সংকলন সুত্তা নিপাতা; এবং কোনও ব্যক্তির কম্ম (কাজ) ) কীভাবে তার ভবিষ্যৎ সত্তাকে প্রভাবিত করে দেখানোর জন্যে বুদ্ধের অতীত জীবন ও তাঁর সহচরগণ সম্পর্কিত কাহিনী জাতকা।
[২] বিনয়া পিতাকা, সন্ন্যাসীদের অনুশীলন গ্রন্থ যা শাস্ত্রবিধি গ্রন্থিত করে। এটি তিন ভাগে বিভক্ত:
[১] সুত্তা বিভঙ্গা: পাক্ষিক সভায় অবশ্যই স্বীকার্য ২২৭টি অপরাধের তালিকা। প্রত্যেকটি নিয়ম কেমন করে এল তার ব্যাখ্যাসহ ধারাভাষ্য।
[২] খন্দকা: মহাভাগ্য (মহান সিরিজ) ও কুলাভাগ্য (ক্ষুদ্র সিরিজ)-এ বিভক্ত এগুলো, বৃত্তিতে যোগ দেওয়ার নিয়মকানুন, জীবনাচার ও উৎসবের উপায় বাৎলে দেয়। নিয়মের উৎসের ঘটনা ব্যাখ্যা করে ধারাভাষ্যও রয়েছে। প্রতিটি বিধিকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া ধারাভাষ্য বুদ্ধ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ কিংবদন্তী সংরক্ষণ করেছে।
[৩] পরিবার: বিধিমালার সার ও শ্রেণীবদ্ধ করণ।
‘তৃতীয় ঝুড়ি’ (অভিধম্ম পিতাকা) দার্শনিক ও মতবাদ বিষয়ক বিশ্লেষণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। জীবনীকারের এতে তেমন আগ্রহ নেই।
দ্বিতীয় সম্মেলনের পর বৌদ্ধ আন্দোলনে মতবিভেদ দেখা দেয়। কয়েকটি গোত্রে ভাগ হয়ে যায় তা। প্রতিটি মতবাদই এইসব প্রাচীন টেক্সট গ্রহণ করে কিন্তু সেগুলোকে নিজস্ব শিক্ষা অনুযায়ী আবার সাজিয়ে নেয়। সাধারণভাবে কোনও কিছুই পরিত্যাগ করা হয়নি বলেই মনে হয়। যদিও সংযোগ এবং পরিবর্ধনের ঘটনা রয়েছে। স্পষ্টতই থেরাভেদা মতবাদের ধর্মগ্রন্থ পালি লিপিই তিপিতাকার একমাত্র ভাষ্য ছিল না, বরং কেবল এটাই অক্ষতভাবে টিকে গেছে। তারপরও হারিয়ে যাওয়া কিছু ভারতীয় রচনা ধর্মগ্রন্থের পরবর্তী সময়ের চীনা অনুবাদে বা তিব্বতী ধর্মগ্রন্থে বিচ্ছিন্নভাবে পাওয়া যায়, যা আমাদের সংস্কৃত টেক্সটের আদি সংকলন তুলে ধরে। সুতরাং সিই পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে বুদ্ধের মৃত্যুর প্রায় হাজার বছর পর এসব অনুবাদ রচিত হলেও কিছু কিছু অংশ পালি লিপির মতোই প্রাচীন এবং তাকে সমর্থন করে।
এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে বেশ কয়েকটা বিষয় বেরিয়ে আসে যা আমরা যেভাবে ধর্মগ্রন্থের বিষয়বস্তুর শরণাপন্ন হচ্ছি তাকে প্রভাবিত করবে। প্রথমত, টেক্সটসমূহ বুদ্ধের নিজস্ব বাণীর সহজ সংকলন হিসাবে বোঝানো হয়েছে, এখানে সন্ন্যাসীদের পক্ষ হতে কোনও কর্তৃত্বপূর্ণ রচনার অংশ যুক্ত হয়নি। মৌখিক প্রেরণ প্রক্রিয়া ব্যক্তিক রচনাশৈলী রহিতঃ এইসব রচনা গস্পেল সম্পর্কে নিজস্ব স্বভাবজাত ব্যাখ্যা দানকারী ম্যাথু, মার্ক, ল্যুক ও জন নামে পরিচিত ইভেঞ্জালিস্টদের সমমর্যাদার কোনও বৌদ্ধের রচনা নয়। যেসব সন্ন্যাসী এসব টেক্সট সংকলিত করেছেন তাঁদের সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। পরবর্তী সময়ে যাঁরা নিজেদের লেখার কাজে নিয়োজিত করেছেন, জানি না তাঁদের সম্পর্কেও। দ্বিতীয়ত, পালি লিপি অবধারিতভাবে থেরাভাদীয় মতবাদ তুলে ধরে। হয়তো যুক্তির স্বার্থে আদি রূপকে বিকৃত করে থাকবে। তৃতীয়ত, সন্ন্যাসীদের যোগ-লব্ধ অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সত্ত্বেও এই ধরনের হস্তান্তর প্রক্রিয়া অনিবার্যভাবে ত্রুটিপূর্ণ ছিল। সম্ভবত বহু রসদ হারিয়ে গেছে, কিছু কিছু ভুল বোঝা হয়েছে এবং নিঃসন্দেহে সন্ন্যাসীদের পরবর্তী দৃষ্টিভঙ্গি বুদ্ধের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে। এসব হিতোপদেশের কোনগুলো নির্ভুল ও কোনগুলো বানোয়াট, জানবার কোনও উপায় আমাদের নেই। আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক ইতিহাসের প্রয়োজন মেটানোর মতো তথ্য ধর্মগ্রন্থসমূহ আমাদের যোগায় না। এসব কেবল গৌতমের মৃত্যুর মোটামুটি তিন প্রজন্ম পরে তাঁর অস্তিত্ব সম্পর্কিত কিছু কিংবদন্তীর অস্তিত্ব দাবি করতে পারে, যখন পালি লিপি সুনির্দিষ্ট রূপ ধারণ করেছিল। পরবর্তী কালের তিব্বতিয় ও চীনা ধর্মগ্রন্থগুলো নিশ্চিতভাবে প্রাচীন রসদ ধারণ করলেও সেগুলোও কিংবদন্তীর আরও পরের পর্যায়কে তুলে ধরে। এছাড়া, এই সত্যটিও রয়েছে যে, রক্ষাপ্রাপ্ত প্রাচীনতম পালি পাণ্ডুলিপির বয়স মাত্র ৫০০ বছর।
তবে আমাদের হতাশ হওয়ার কারণ নেই। টেক্সটসমূহ ঐতিহাসিক উপাদান ধারণ করে যা বিশ্বস্ত বলে মনে হয়। বিসিই পঞ্চম শতাব্দীর উত্তর ভারত সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারি আমরা, যার সঙ্গে বুদ্ধের সমসাময়িক জৈনদের ধর্মগ্রন্থ মিলে যায়। টেক্সটে বেদ-ধর্মের নির্ভুল উল্লেখ রয়েছে, যার সম্পর্কে পরবর্তী কালের ধর্মগ্রন্থ ও ধারাভাষ্যের রচয়িতা বেশ অজ্ঞ ছিলেন; মঘদের রাজা বিম্বিসারার মতো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে জানতে পারি আমরা, নগর জীবনের উন্মেষ ও সেই আমলের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও জানতে পারি; প্রত্নতাত্ত্বিক, ভাষাবিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদদের আবিষ্কারের সঙ্গে এসব মিলে যায়। পণ্ডিতরা এখন নিশ্চিত যে, সম্ভবত এইসব ধর্মীয় উপাদানের কিছু কিছু একেবারে আদি বৌদ্ধ মতবাদের সমসাময়িক। বুদ্ধ স্রেফ বৌদ্ধদের আবিষ্কার, ঊনবিংশ শতাব্দীর এমন দৃষ্টিভঙ্গি আজ মেনে নেওয়া কঠিন বিপুল শিক্ষার ভেতর একটি আদি বুদ্ধিমত্তার দিকে নির্দেশকারী এক ধরনের সামঞ্জস্যতা রয়েছে, রয়েছে সম্পর্ক। এগুলোকে সমন্বিত সৃষ্টি হিসাবে চিন্তা করা কঠিন। এমন ঘটা অসম্ভব নয় যে এসব বাণীর কিছু কিছু সত্যিই খোদ সিদ্ধার্থ গৌতমের উচ্চারণ ছিল, যদিও সেগুলো ঠিক কোনগুলো সে ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারব না আমরা।
পালি লিপির এই বর্ণনা হতে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে আসে: এখানে বুদ্ধের জীবনের কোনও ধারাবাহিক বিবরণ নেই। ছোট ছোট ঘটনার সাথে শিক্ষার উল্লেখ করা হয়েছে এবং স্রেফ কোনও নিয়ম বা মতবাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। কখনও কখনও হিতোপদেশে বুদ্ধ সন্ন্যাসীদের কাছে নিজের পূর্ব-জীবন বা আলোকপ্রাপ্তির কথা বলেছেন। কিন্তু ইহুদি ও ক্রিশ্চান ঐশিগ্রন্থে মোজেস বা জেসাসের জীবন বৃত্তান্তের মতো উন্নত সময়ানুক্রমিক কোনও বিবরণ নেই। পরবর্তী সময়ে বুদ্ধরা পরিবর্ধিত, ধারাবাহিক জীবনী রচনা করেছে। আমাদের কাছে তিব্বতীয় ললিতা-বিস্তারা (সিই তৃতীয় শতাব্দী) এবং পালি নিদান কথা রয়েছে (সিই পঞ্চম শতাব্দী), জাতকা কাহিনীর ধারাভাষ্যের রূপ ধারণ করেছে এগুলো। সিই পঞ্চম শতকে থেরাভাদীয় পণ্ডিত বুদ্ধগোসা কর্তৃক চূড়ান্ত রূপ দেওয়া বিধিবিধানের পালি ধারাভাষ্যও পাঠককে বিধি-বিধানে বর্ণিত বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড খণ্ড ঘটনাবলীকে সময়ানুক্রমে সাজাতে সাহায্য করেছে। কিন্তু এসব পরিবর্ধিত বিবরণেও ফাঁক রয়েছে। এগুলোয় বুদ্ধের আলোকপ্রপ্তির পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ বছরের শিক্ষাব্রতের কোনও বিস্তারিত বর্ণনা নেই। ললিতা-বিস্তারা শেষ হয়েছে বুদ্ধের প্রথম হিতোপদেশ দিয়ে; এবং নিদান কথার সমাপ্তি ঘটেছে শিক্ষাব্রতের সূচনায় কোসালার রাজধানী সাবাস্তিতে প্রথম বুদ্ধ বসতির গোড়াপত্তনের ভেতর দিয়ে। বুদ্ধের ব্রতের আরও বিশ বছর সময় রয়েছে যার সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না।
এসব যেন যেসব বৌদ্ধ ঐতিহাসিক বুদ্ধের কাহিনী অপ্রাসঙ্গিক দাবি করে তারাই সঠিক, এমন ইঙ্গিতই করে। একথাও সত্যি যে উত্তর ভারতের অধিবাসীরা আমাদের মতো ইতিহাসে আগ্রহী ছিল না। তারা ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর তাৎপর্য নিয়েই বেশি উদ্বিগ্ন ছিল। ফলে ধর্মগ্রন্থসমূহ অধিকাংশ পশ্চিমারা যাকে অপরিহার্য মনে করবে সেসব বিষয়ে খুব সামান্য তথ্যই যোগায়। আমরা এমনকি বুদ্ধ কোন শতাব্দীতে জীবন যাপন করেছেন সেটাও নিশ্চিত হতে পারি না। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, আনুমানিক বিসিই ৪৮৩ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। কিন্তু চীনা উৎসগুলো ধারণা দেয়, আরও পরে, বিসিই ৩৬৮ অব্দেও মারা গিয়ে থাকতে পারেন তিনি। খোদ বৌদ্ধরাই তাঁর জীবন সম্পর্কে এমন উদাসীন হয়ে থাকলে গৌতমের জীবনী নিয়ে কেন মাথা ঘামাতে যাবে কেউ?
কিন্তু কথাটা পুরোপুরি সত্যি নয়। পণ্ডিতগণ এখন বিশ্বাস করেন যে, দ্বিতীয় সম্মেলনকালে রচিত গৌতমের জীবনের একটি হারিয়ে যাওয়া আদি বিররণের ভিত্তিতেই পরবর্তী সময়ের পরিবর্ধিত জীবনীগুলো রচিত। এছাড়া, ধর্মগ্রন্থসমূহ দেখায়, আদি বৌদ্ধরা গৌতমের জীবনীর কিছু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত নিয়ে গভীর চিন্তা করেছে: তাঁর জন্ম, স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনযাপন পরিহার, আলোকপ্রাপ্তি, শিক্ষাব্রতের সূচনা ও পরলোকগমন। এসব ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গৌতমের জীবনীর কিছু দিক সম্পর্কে আমরা হয়তো অন্ধকারে থাকতে পারি, কিন্তু এসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় ফুটে ওঠা সাধারণ কাঠামোর সঠিকতা সম্পর্কে নিশ্চিত থাকা যেতে পারে। বুদ্ধ সবসময় জোর দিয়ে বলেছেন, তাঁর শিক্ষাসমূহ সম্পূর্ণই নিজস্ব অভিজ্ঞতা ভিত্তিক। তিনি অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গি যাচাই করেননি বা কোনও বিমূর্ত তত্ত্বের বিকাশ ঘটাননি। নিজের জীবন-ইতিহাস হতে নিজস্ব সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তিনি শিষ্যদের শিখিয়েছেন যে, আলোকপ্রাপ্ত হতে হলে তাদের অবশ্যই গৃহত্যাগ করে ভিক্ষু-সন্ন্যাসী হতে হবে, যোগের মানসিক অনুশীলন অনুসরণ করতে হবে-যেমন তিনি করেছেন। তাঁর জীবন ও শিক্ষা অবিচ্ছেদ্য। তাঁর দর্শন অনিবার্যভাবে আত্মজীবনীমূলক। অন্য বৌদ্ধদের জন্যে আদর্শ ও অনুপ্রেরণা হিসাবে ধর্মগ্রন্থে তাঁর জীবনের মূল কাঠামো বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি যেমন বলেছেন: ‘যে আমাকে দেখে সে ধম্মকে (শিক্ষা) দেখে আর যে ধম্ম দেখে সে আমাকেই দেখে।’
এখানে এমন একটি ধারণা রয়েছে যা সব প্রধান ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের বেলায়ই সত্যি। আধুনিক নিউ টেস্টামেন্ট পণ্ডিতগণ দেখিয়েছেন, আমরা যতটা ধারণা করি আসলে ঐতিহাসিক জেসাস সম্পর্কে তার চেয়ে অনেক কম জানি। আমরা যেমন মনে করি, ‘গস্পেল-সত্যি’ আসলে মোটেই তেমন নিরেট নয়। কিন্তু তা লক্ষ লক্ষ মানুষের নিজেদের জীবনকে জেসাসের অনুসরণে গড়ে তুলতে ও নতুন জীবন ধারণের উপায় হিসাবে তাঁর সহমর্মিতা ও কষ্ট ভোগের পথ অনুসরণের বেলায় বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। জেসাস ক্রাইস্ট অবশ্যই ছিলেন, কিন্তু গস্পেলসমূহে উদাহরণ হিসাবে তাঁর কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। ক্রিশ্চানরা তাদের নিজস্ব সমস্যার মূলে চোখ ফেরানোর সময় তাঁর শরণাপন্ন হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কেউ ব্যক্তিগত রূপান্তরের অভিজ্ঞতা লাভ করলেই কেবল তার পক্ষে পুরোপুরিভাবে জেসাসকে উপলব্ধি করা সম্ভব। বুদ্ধের ক্ষেত্রেও একথা সত্যি: যিনি সম্ভবত বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সর্বকালের অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর শিক্ষা ১,৫০০ বছর ধরে ভারতে বিকাশ লাভ করে, তারপর তিব্বত, মধ্য এশিয়া, চীন কোরিয়া, জাপান ও দক্ষিণ এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে। লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে তিনি মানবীয় অবস্থার প্রতীক ছিলেন।
এতে বোঝা যায় বুদ্ধের জীবন উপলব্ধি, যার কিয়দংশে তাঁর শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত, আমাদেরও মানুষের সংকট উপলব্ধিতে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু এটা সাধারণভাবে একবিংশ শতাব্দীতে যেসব জীবনী রচিত হয়ে থাকে তেমন কিছু হতে পারবে নাঃ প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছিল তা উদ্ধার বা বুদ্ধের জীবন সম্পর্কে বিতর্কিত নতুন তথ্য আবিষ্কার করবে না এটা, কারণ আমরা সততার সঙ্গে ঐতিহাসিক সত্য হিসাবে নিশ্চিত করতে পারব, ধর্মগ্রন্থসমূহে এমন একটি ঘটনাও নেই ঘটনাও নেই। কিংবদন্তীর সত্যটুকুই ঐতিহাসিক। আমাদের অবশ্যই বুদ্ধের মৃত্যুর প্রায় শত বছর পর পালি টেক্সটসমূহ চূড়ান্ত রূপ নেওয়ার সময় যেভাবে প্রকাশ পেয়েছিল সেভাবেই সমগ্র কিংবদন্তীকে গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে বহু পাঠকই এই কিংবদন্তীর বৈশিষ্ট্যকে অবিশ্বাস্য মনে করবেন: গৌতমের জীবনে অধিকতর জাগতিক ও ঐতিহাসিক সম্ভাব্য ঘটনাবলীর সঙ্গে দেবতার কাহিনী ও অলৌকিক ঘটনাবলী স্থান পেয়েছে। আধুনিক ঐতিহাসিক সমালোচনায় অতিলৌকিক ঘটনাবলীকে পরবর্তী সময়ের সংযোজন বিবেচনায় বাদ দেওয়াই সাধারণ গৃহীত নিয়ম। কিন্তু পালি বিধানের ক্ষেত্রে আমরা তা করতে গেলে কিংবদন্তীকে বিকৃত করা হবে। অধিকতর স্বাভাবিক ঘটনাগুলো এইসব তথাকথিত নিদর্শন ও বিস্ময়কর ঘটনাসমূহের তুলনায় কিংবদন্তীর আদিরূপ কিনা নিশ্চিত হতে পারব না আমরা। বিধি-বিধানের বিকাশকারী সন্ন্যাসীগণ নিশ্চিতভাবে দেবতার বিশ্বাস করতেন, যদিও তাঁদের সীমাবদ্ধ সত্তা হিসাব দেখেছেন; এবং আমরা যেমন দেখব, তাঁদের মানবীয় মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার অভিক্ষেপ হিসাবে দেখতে শুরু করেছিলেন। তাঁরা আরও বিশ্বাস করতেন যে, যোগে দক্ষতা যোগীকে অসাধারণ ‘অলৌকিক’ ক্ষমতা (ইদ্ধি) দেয়। যোগ অনুশীলন এমনভাবে মনকে প্রশিক্ষিত করে যে তা ব্যতিক্রমী কর্মকাণ্ড দেখাতে পারে, ঠিক যেমন অলিম্পিক অ্যাথলিটকে সাধারণ মরণশীলের অতিরিক্ত ক্ষমতা যোগায়। লোকে ধরে নিত যে, একজন দক্ষ যোগী শূন্যে ভাসতে পারে, মানুষের মনের কথা পড়তে পারে ও ভিন্ন লোকে গমন করতে পারে। বিধি-বিধান সংকলক সন্ন্যাসীগণ হয়তো বুদ্ধ এসব কাজে সক্ষম বলে প্রত্যাশা করে থাকবেন, যদিও ইদ্ধি সম্পর্কে তাঁর তীর্যক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। এসব এড়িয়ে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন তিনি আমরা যেমন দেখব, ‘অলৌকিক কাহিনীগুলো’ প্রায়শঃই সতর্কতামূলক গল্প, এজাতীয় আধ্যাত্মিক প্রদর্শনবাদীতার অর্থহীনতা তুলে ধরার লক্ষ্যেই রচিত।
পালি ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ কাহিনীগুলোর অনেকগুলোরই রূপক বা প্রতীকী অর্থ রয়েছে। আদি বৌদ্ধরা ধর্মগ্রন্থে ঐতিহাসিকভাবে নির্ভুল বর্ণনার চেয়ে তাৎপর্যের সন্ধান করেছে। আমরা এও দেখব, নিদান কথার মতো প্রাপ্ত পরবর্তী সময়ের জীবনীসমূহ পালি বিধি-বিধানের অধিকতর বিচ্ছিন্ন এবং প্রায়গিক বিবরণের তুলনায় গৌতমের পিতৃগৃহ ত্যাগের সিদ্ধান্ত বা তাঁর আলোকপ্রাপ্তির মতো ঘটনাবলীর বিকল্প ও অধিকতর বিস্তারিত বিবরণ দেয়। পরবর্তী সময়ের এইসব কাহিনীও বিধি-বিধানের পৌরাণিক উপাদানের চেয়ে অনেক সমৃদ্ধঃ দেবতার আবির্ভাব হচ্ছে, পৃথিবী কাঁপছে, অলৌকিকভাবে দরজা খুলে যাচ্ছে। আবার এমনটা মনে করা ভুল হবে যে, এসব অলৌকিক বর্ণনা আদি কিংবদন্তীর সঙ্গে যোগ করা হয়েছে। পরবর্তী কালের এইসব জীবনী সম্ভবত বুদ্ধের মৃত্যুর শত বছর পর রচিত নিখোঁজ জীবনীর উপর ভিত্তি করে রচিত, একই সময়ে বিধি-বিধান নির্দিষ্ট রূপ পেয়েছিল। এই স্পষ্ট পৌরাণিক কাহিনীগুলো বিধানের কাহিনীর চেয়ে ভিন্ন ছিল বলে আদি বৌদ্ধদের উদ্বিগ্ন করে তোলেনি। এগুলো ছিল এইসব ঘটনার আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক অর্থ প্রকাশকারী স্রেফ ভিন্ন ব্যাখ্যা।
কিন্তু এইসব মিথ ও অলৌকিক ঘটনাবলী দেখায় যে, বুদ্ধকে স্রেফ একজন পধপ্রদর্শক ও দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী হিসাবে দেখা উচিৎ বলে যারা বিশ্বাস করতেন সেই থোরাভাদীয় সন্ন্যাসীরাও তাঁকে অতিমানব হিসাবে দেখতে শুরু করেছিলেন। অধিকতর জনপ্রিয় মহায়না মতবাদ কার্যত গৌতমকে দেবতায় পরিণত করেছে। মনে করা হতো যে, থেরাভেদা বৌদ্ধ মতবাদের খাঁটি রূপ তুলে ধরে আর মহায়না ছিল বিকৃত। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতরা মনে করেন উভয়ই সঠিক। থেরাভেদা যোগের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে গেছে এবং বুদ্ধের মতো আলোকপ্রাপ্ত আরাহান্তে (‘সফল জন’) পরিণত সন্ন্যাসীদের সম্মান প্রদর্শন করেছে। কিন্তু মহায়নায় বুদ্ধকে মানুষের জীবনে চিরন্তন সত্তা এবং উপাসনার বস্তু হিসাবে শ্রদ্ধাকারীরা পালি টেক্সটে জোরের সঙ্গে গুরুত্ব দেওয়া অন্যান্য মূল্যবোধ, বিশেষত সহমর্মিতার গুরুত্ব সংরক্ষণ করেছে। তারা মনে করেছে থেরাভেদা বড় বেশি বিশেষায়িত, আরাহান্তরা স্বার্থপরের মতো নিজেদের মাঝে অলোকনকে আঁকড়ে রেখেছেন। তাঁরা বুদ্ধ হওয়ার নিয়তিপ্রাপ্ত কিন্তু ‘বহুজনের’ কাছে মুক্তির বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্যে আলোকন বিলম্বিতকারী নারী-পুরুষ বোধিসত্তাদের শ্রদ্ধা জানাতে পছন্দ করেছেন। আমরা দেখব, এটাই ছিল সন্নাসীদের ভূমিকা সম্পর্কে গৌতমের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি। দুটো মতবাদই গুরুত্বপূর্ণ গুণাবলী আঁকড়ে ধরেছে: দুটোই সম্ভবত কিছু হারিয়েছে।
গৌতম কোনও ব্যক্তিক কাল্ট চাননি, কিন্তু বরং স্বয়ং তিনি, সক্রেটিস, কনফুসিয়াস এবং জেসাসের মতো আদর্শ ব্যক্তিবর্গ দেবতা বা অতিমানবীয় সত্তা হিসাবে পুজিত হয়েছেন। এমনকি পয়গম্বর মুহাম্মদও (স) সবসময় নিজেকে সাধারণ মানুষ হিসাবে দাবি করা সত্ত্বেও মুসলিমরা তাঁকে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ (ইসলাম) সম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে একজন আদর্শ সম্পূর্ণ মানুষ হিসাবে শ্রদ্ধা করে। এইসব মানুষের অস্তিত্বের বিশালতা ও অর্জন সাধারণ মানদণ্ডকে অস্বীকার করে বলে মনে হয়। পালি বিধানে দেখা যায়, গৌতমের জীবনেও এসব ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু এইসব অলৌকিক কাহিনীকে আক্ষরিক অর্থে সত্যি ধরে নেওয়া যাবে না। এগুলো আমাদের মানবীয় সত্তার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ধারণা দেয়। জেসাস, মুহাম্মদ (স) ও সক্রেটিসের মতো বুদ্ধও নারী-পুরুষকে কেমন করে জগৎ ও দুঃখ-কষ্টকে অতিক্রম করা যায়, কীভাবে মানবীয় তুচ্ছতা আর প্রলোভনের ঊর্ধ্বে উঠে পরম মূল্য আবিষ্কার করা যায়, সেই শিক্ষা দিচ্ছিলেন। সকলেই মানুষকে অধিকতর সচেতন করে তুলে তাদের পূর্ণ সম্ভাবনা সম্পর্কে জাগ্রত করে তুলতে চেয়েছেন। এভাবে ক্ষমতাশালী করে তোলা একজন মানুষের জীবনী আধুনিক বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের মানদণ্ডকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। কিন্তু পালি লিপি ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট টেক্সটসমূহে তুলে ধরা আদর্শ ব্যক্তির পর্যালোচনা থেকে আমরা মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে আরও অনেক কিছু জানতে পারি। মানুষের দায়িত্ব সম্পর্কে নতুন দর্শন লাভ করি। একটি ত্রুটিপূর্ণ যন্ত্রণাময় বিশ্বে মানবীয় অবস্থা সম্পর্কে একটি ভিন্ন ধরনের সত্যের রূপরেখা তুলে ধরে এইসব উদাহরণমূলক কাহিনীগুলো।
তবে বুদ্ধের জীবনীর আরও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, গস্পেলসমূহ স্বভাবসহ জেসাসের একটি স্পষ্ট ব্যক্তি সত্তা তুলে ধরে: বাকধারা, বিশেষ বাঁক, আবেগ ও সংগ্রামের গম্ভীর মুহূর্ত, দৃঢ়তা, আতঙ্ক ও ভয় ধরে রাখা হয়েছে এখানে। বুদ্ধের ক্ষেত্রে এটি সত্যি নয়। তাঁকে ব্যক্তির চেয়ে বরং ধরণ হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাঁর আলোচনায় আমাদের আনন্দিত করে তোলা জেসাস বা সক্রেটিসের ভাষণের আকস্মিক সরল মন্তব্য, জোর ধাক্কা, রসালো উক্তির কোনওটাই পাই না। তিনি ভারতীয় দার্শনিক চাহিদা অনুসারে কথা বলেন: গম্ভীর, আনুষ্ঠানিক, নৈর্ব্যক্তিক। আলোকপ্রাপ্তির পর আমরা তাঁর পছন্দ-অপছন্দ, আশা-আশঙ্কা, হতাশার মুহূর্ত, উদ্বেলিত হওয়া বা গভীর সংগ্রাম সম্পর্কে কিছুই ধারণা করতে পারি না। অবশিষ্ট রয়ে গেছে কেবল অতিমানবীয় নীরবতা, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ, ব্যক্তিগত পছন্দের অতীত এক ধরনের মহত্ব ও গভীর প্রশান্তি। বুদ্ধকে প্রায়শঃই অমানবিক সত্তা–পশু, গাছপালা কিংবা মহীরুহের সঙ্গে তুলনা করা হয়–সেটা তিনি মানবেতর বা অমানবিক বলে নয় বরং তিনি আমরা যে স্বার্থপরতাকে আমাদের অবস্থার সঙ্গে অনিবার্য মনে করি তাকে ছাড়িয়ে যেতে পেরেছেন বলে। বুদ্ধ মানুষ হওয়ার এক নতুন উপায়ের সন্ধান করছিলেন। পশ্চিমে আমরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও আত্ম-প্রকাশকে মূল্য দিই, কিন্তু এটা সহজেই আত্ম-প্রসাদে পরিণত হতে পারে। গৌতমের মাঝে আমরা পূর্ণাঙ্গ ও শ্বাসরুদ্ধকর আত্মত্যাগ লক্ষ করি। ধর্মগ্রন্থসমূহ তাঁকে একজন পরিপূর্ণ ‘ব্যক্তিত্ব’ হিসাবে তুলে ধরেনি জানতে পারলে অবাক হতেন না তিনি, বরং হয়তো বলতেন ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের ধারণা বিপজ্জনকভাবে মোহ। তিনি হয়তো বলতেন, তাঁর জীবনে অসাধারণ কিছু নেই। তাঁর আগেও অন্য বুদ্ধরা ছিলেন, যাঁদের প্রত্যেকেই একই ধৰ্ম্ম প্রচার করেছেন। একই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তাঁরাও। বুদ্ধ ট্র্যাডিশন এই ধরনের পঁচিশজন আলোকপ্রাপ্ত মানুষের অস্তিত্ব দাবি করে। বর্তমান ঐতিহাসিক যুগ শেষে, যখন এই অত্যাবশ্যকীয় সত্যের জ্ঞান ক্ষীণ হয়ে আসবে, মেত্তায়া নামে একজন নতুন বুদ্ধ আসবেন পৃথিবীতে। তিনিও একই জীবনচক্র অতিক্রম করবেন। বুদ্ধের এই আদিরূপের ধারণা এতই জোরাল যে নিদান কথায় পিতৃগৃহ হতে তাঁর ‘বহির্গমন’ সম্পর্কিত বিখ্যাত উপাখ্যানটিকে পালি শাস্ত্রে গৌতমের অন্যতম পূর্বসুরি বুদ্ধ বিপাসসির জীবনে ঘটার দাবি করা হয়েছে। ধর্মগ্রন্থসমূহে গৌতমের অসাধারণ, ব্যক্তিগত অর্জন সম্পর্কে নয়, বরং সকল বুদ্ধ, সকল মানুষের আলোকপ্রাপ্তির সন্ধানকালে অবশ্য অনুসরণীয় উপায় সম্পর্কে আগ্রহী।
গৌতমের কাহিনীর সঙ্গে আমাদের কালের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। আমরাও বিসিই ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীর উত্তর ভারতের মতো পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি। উত্তর ভারতীয় জনগণের মতো আবিষ্কার করছি যে, পবিত্রকে অনুভব করার প্রথাগত উপায় ও আমাদের জীবনের পরম অর্থ আবিষ্কার কঠিন কিংবা অসম্ভব। ফলস্বরূপ, আধুনিক অভিজ্ঞতায় শূন্যতা একটি অত্যাবশ্যকীয় অংশ হয়ে রয়েছে। গৌতমের মতো এক রাজনৈতিক সহিংসতার যুগে বাস করছি আমরাও। মানুষের প্রতি মানুষের ভীতিকর অমানবিক আচরণ লক্ষ করছি। আমাদের সমাজেও ব্যাপক অস্থিরতা, নাগরিক হতাশা ও বৈষম্য রয়েছে। অনেক সময় বিকাশমান নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা নিয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠি আমরা।
বুদ্ধের অনুসন্ধানের বহু দিকই আধুনিক মূল্যবোধের কাছে আবেদন সৃষ্টি করবে। তাঁর সচেতন অভিজ্ঞতাবাদ এবং সেই সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আমাদের নিজস্ব পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বাস্তব সুরের সঙ্গে বিশেষভাবে মানানসই, যারা অতিপ্রাকৃত ঈশ্বরের ধারণাকে অচেনা বলে মনে করেন তাঁরাও বুদ্ধের পরম সত্তার অস্তিত্ব মানতে অস্বীকৃতিকে কাছে টেনে নেবেন। নিজ গবেষণাকে তিনি মানবীয় প্রকৃতির মাঝে সীমাবদ্ধ রেখেছেন এবং বরাবর জোর দিয়েছেন যে তাঁর অভিজ্ঞতা–এমনকি নির্বাণের পরম সত্যিও–মানবীয় প্রকৃতির সঙ্গে পুরোপুরি স্বাভাবিক। প্রাতিষ্ঠানিক ধার্মিকতার কোনও কোনও ধরনের অসহিষ্ণুতায় ক্লান্ত যারা, তারাও বুদ্ধের সহমর্মিতা ও প্রেমময় ভালোবাসার উপর গুরুত্ব প্রদানকে স্বাগত জানাবেন।
কিন্তু বুদ্ধ একটি চ্যালেঞ্জও, কেননা আমাদের অধিকাংশের চেয়ে অনেক বেশি রেডিক্যাল তিনি। আধুনিক সমাজে একটা নতুন অর্থডক্সির প্রকাশ ঘটছে যাকে অনেক সময় ‘ইতিবাচক চিন্তা’ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়। সবচেয়ে খারাপ, আশাবাদের এই অভ্যাস আমাদের আবেগগত রক্ষা নিশ্চিত করতে বালিতে মাথা লুকাতে সাহায্য করে, নিজের এবং অন্যদের যন্ত্রণার সর্বব্যাপীতা অস্বীকার করায় ও আমাদের ইচ্ছাকৃত হৃদয়হীনতায় রুদ্ধ করতে প্ররোচিত করে। বুদ্ধ এসবে মাথা ঘামাতেন না। তাঁর চোখে মানুষ যতক্ষণ দুঃখকষ্টের বাস্তবতায় আক্রান্ত না হচ্ছে, যতক্ষণ না বুঝতে পারছে আমাদের সমগ্র অস্তিত্বে কীভাবে তা প্রবাহিত হচ্ছে, অন্য মানুষের, এমনকি যাদের আন্তরিক মনে হয় না তাদেরও, যন্ত্রণা অনুভব করতে না পারছে ততক্ষণ আধ্যাত্মিক জীবন সূচিত হতে পারে না। একথাও ঠিক যে, আমাদের বেশিরভাগই বুদ্ধের আত্ম-পরিত্যাগের মাত্রায় পৌঁছতে প্রস্তুত নই। আমরা জানি অহমবোধ খারাপ; আমরা জানি বিশ্বের সকল মহান ট্রাডিশন–কেবল বুদ্ধ মতবাদ নয়–আমাদের স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে ওঠার তাগিদ দিয়েছে। কিন্তু আমরা যখন মুক্তির সন্ধান করি–ধর্মীয় বা সেক্যুলার রূপে–আমরা আসলে আমাদের সত্তার বোধ উন্নত করতে চাই। ধর্ম হিসাবে স্বীকৃত অনেক কিছুই প্রায়শঃ বিশ্বাসের প্রবর্তকগণ যে অহমকে বিসর্জন দিতে বলেছেন সেটাকেই প্রতিষ্ঠিত করতে বা উন্নত করার জন্যেই সৃষ্টি হয়। আমরা ধরে নিই বুদ্ধের মতো একজন মানুষ দৃশ্যতঃ ব্যাপক সংগ্রামের পর সবরকম স্বার্থপরতা বিসর্জন দিয়ে অসামরিক, রসহীন এবং গম্ভীর হয়ে উঠবেন।
কিন্তু বুদ্ধের ক্ষেত্রে তা সত্যি নয় বলে মনে হয়। তিনি নৈর্ব্যক্তিক হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু তাঁর অর্জিত অবস্থা যারা তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন তাঁদের সবার মাঝেই এক অসাধারণ আবেগ সৃষ্টি করেছে। বুদ্ধের অর্জিত কোমলতা, ন্যায্যতা, মহত্ব, নিরপেক্ষতা ও প্রশান্তির বিরামহীন এমনকি নির্মম মাত্রা আমাদের হৃদয়ের তন্ত্রীকে নাড়া দেয় ও গভীরতম আকাঙ্ক্ষায় অনুরণন সৃষ্টি করে। মানুষ তাঁর নিরাবেগ স্থৈর্য্যে বিকর্ষিত হয়নি, কোনও বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি দুর্বলতার অভাবে নিরুৎসাহিত হয়নি। বরং তারা বুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, তাঁর চারপাশে ভীড় জমিয়েছে।
লোকে যখন দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের জন্যে তাঁর বাৎলে দেওয়া উপায় বেছে নেয়, তারা বলে ‘বুদ্ধের কাছে আশ্রয়’ নিয়েছে। কোলাহলময় অহমবাদের সহিংস পৃথিবীতে তিনি ছিলেন শান্তির স্বর্গ। পালি লিপির একটি আবেগময় কাহিনীতে তীব্র হতাশাগ্রস্ত এক রাজা বিশাল বিশাল ট্রপিক্যাল গাছপালায় ভর্তি একটা পার্কের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। শকট ছেড়ে প্রায় মানুষ সমান লম্বা বিরাট বিরাট শেকড়ের মাঝে হাঁটছিলেন তিনি। ওগুলোর ‘আস্থা ও বিশ্বাস’ সৃষ্টির কায়দা লক্ষ করলেন তিনি। ‘ওরা ছিল শান্ত: বেসুরো কোনও কণ্ঠ ওদের শান্তি বিনষ্ট করেনি, সাধারণ জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার বোধ যুগিয়েছে ওগুলো, এমন একটা জায়গা যেখানে কেউ মানুষের থেকে দূরে আশ্রয় নিতে পারে’ ও জীবনের নিষ্ঠুরতা হতে অবসর পেতে পারে। চমৎকার প্রাচীন গাছগুলো দেখার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধের কথা মনে পড়ে যায় রাজার, লাফিয়ে শকটে উঠে বহু মাইল দূরে বুদ্ধের বাড়িতে না পৌঁছা পর্যন্ত শকট হাঁকিয়ে যান। জগৎ থেকে ভিন্ন শান্তির জায়গার সন্ধান, জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন কিন্তু বিস্ময়করভাবে অভ্যন্তরে অবস্থিত, নিরপেক্ষ, সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত, শান্ত, আমাদের যা সকল সংকটের প্রতিকূলে আমাদের জীবনে একটা মূল্য আছে, এমন একটা বিশ্বাসে পরিপূর্ণ করে, যাকে অনেকে খোঁজে, বাস্তবে আমরা তাকে বলি ‘ঈশ্বর’। সত্তার সীমাবদ্ধতা ও পক্ষপাতিত্ব অতিক্রম করে যাওয়া বুদ্ধের মাঝে বহু মানুষই যেন তার দেখা পেয়েছে বলে মনে হয়। বুদ্ধের জীবন আমাদের শক্তিশালী কিছু বিশ্বাসকে চ্যালেঞ্জ করে, কিন্তু তা আবার আলোকবর্তিকাও হতে পারে। আমরা হয়তো তাঁর বাৎলে দেওয়া পদ্ধতি পুরোপুরি অনুসরণ করতে পারব না, কিন্তু তাঁর উদাহরণ কিছু কিছু উপায় আলোকিত করে যার সাহায্যে আমরা এক উন্নত ও সত্যিকার অর্থে সহানুভূতিময় মানবতার দিকে অগ্রসর হতে পারি।
দ্রষ্টব্য: বুদ্ধের ধর্মগ্রন্থসমূহ হতে উদ্ধৃত করার সময় আমি অন্যান্য পণ্ডিতদের অনুবাদের সাহায্য নিয়েছি। তবে সেগুলোকে নিজের মতো প্রকাশ করেছি এবং পশ্চিমা পাঠকদের কাছে বোধগম্য করে তোলার জন্যে আমার নিজস্ব ভাষ্য তৈরি করেছি। বুদ্ধ মতবাদের কিছু মূল্যবান শব্দ এখন সাধারণ ইংরেজি ডিসকোর্সে নৈমিত্তিক হয়ে গেছে, কিন্তু আমরা সাধারণত পালি ধরনের পরিবর্তে সংস্কৃতকেই বেছে নিয়েছি। সামঞ্জস্যতার স্বার্থে আমি পালিতে স্থির থেকেছি, ফলে পাঠক, উদাহরণ স্বরূপ, কর্ম, ধর্ম এবং নির্বাণের বদলে কৰ্ম্ম, ধম্ম এবং নিব্বানা দেখতে পাবেন।
১. গৃহত্যাগ
বিসিই ষষ্ঠ শতকের শেষ দিকে এক রাতে সিদ্ধার্থ গৌতম নামে এক যুবক হিমালয়ের পাদদেশে কাপিলাবাস্তুর আরামদায়ক বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসে পথে নামলেন।[১] আমাদের বলা হচ্ছে তাঁর বয়স ছিল ঊনত্রিশ বছর। কাপিলাবাস্তুর অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন তাঁর বাবা, গৌতম চাইতে পারেন এমন সমস্ত বিলাসিতা দিয়ে তাঁকে ঘিরে রেখেছিলেন তিনি। স্ত্রী ছিল তাঁর, আর মাত্র কয়েকদিন বয়সী একটা ছেলে। কিন্তু ছেলের জন্মের মুহূর্তে এতটুকু আনন্দ বোধ করেননি গৌতম। ছেলেকে তিনি রাহুলা বা ‘বাঁধন’ নামে ডেকেছেন; তাঁর বিশ্বাস ছিল শিশুটি তাঁকে ঘৃণিত হয়ে ওঠা জীবনধারার সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবে।[২] তিনি এক ‘সুপরিসর’ এবং ‘চকচকে খোলসের মতো পূর্ণাঙ্গ ও খাঁটি’ অস্তিত্বের প্রত্যাশী ছিলেন, কিন্তু তাঁর বাবার বাড়িটি অভিজাত, মার্জিত হলেও গৌতমের কাছে সংকীর্ণ, ‘গিজগিজে’ ও ‘ধূলিময়’ মনে হয়েছে। খুচরো কাজকর্ম ও অর্থহীন দায়দায়িত্ব সবকিছূ জীর্ণ করে রেখেছে। ক্রমবর্ধমানহারে নিজেকে এমন এক জীবনযাত্রার আকাঙ্ক্ষা বোধ করছেন বলে আবিষ্কার করছিলেন তিনি যার সঙ্গে সংসার ধর্মের কোনও সম্পর্ক নেই। ভারতের সাধুরা যাকে ‘গৃহত্যাগ’[৩] বলেন। গাঙ্গেয় অববাহিকার উর্বর সমতলের প্রান্তবর্তী নিবিড় বিস্তীর্ণ বনভূমি হাজার হাজার নারী-পুরুষের আশ্রয়ে পরিণত হয়েছিল যারা তাদের মতে ‘পবিত্র জীবন’ (ব্রহ্মাচার্য্য)-এর সন্ধানে পরিবার ত্যাগ করেছিল। এই দলে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন গৌতম!
সিদ্ধান্তটা রোমান্টিক ছিল। কিন্তু তাঁর ভালোবাসার পাত্রদের জন্যে দারুণ বেদনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল সেটা। গৌতমের মা-বাবা, পরে স্মৃতিচারণ করেছেন তিনি, আদরের সন্তানকে সাধুদের পোশাকে পরিণত হওয়া গেরুয়া জোব্বা গায়ে চাপিয়ে মাথা আর দাড়িগোঁফ কামাতে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন।[৪] কিন্তু আমাদের এও বলা হয়েছে যে, বিদায় নেওয়ার আগে ঘুমন্ত স্ত্রী ও ছেলেকে এক নজর দেখবেন বলে জন্যে লুকিয়ে ওপরতলায় ওঠেন তিনি, কিন্তু কোনও রকম বিদায় সম্ভাষণ ছাড়াই আবার সেখান থেকে সরে আসেন।[৫] যেন স্ত্রী থেকে যাবার জন্যে কাকুতি-মিনতি শুরু করলে আপন সিদ্ধান্তে অটল থাকার ব্যাপারে নিজেকে বিশ্বাস করতে পারেননি। এটাই সমস্যার মূল। বনবাসী বহু সন্ন্যাসীর মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, দুঃখ ও বেদনায় ভরপুর এক অস্তিত্বের সঙ্গে বন্দিকারী বস্তু ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্কই তাঁকে যন্ত্রণা ও দুঃখের সাথে বেঁধে দিয়েছে। সন্ন্যাসীদের কেউ কেউ পচনশীল জিনিসের প্রতি আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে আত্মাকে টেনে নামানো মহাবিশ্বের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠে যাওয়া থেকে বিরত রাখা ‘ধুলিকণার’ সঙ্গে তুলনা করেছেন। নিজের বাড়িকে ‘ধূলিময়’ বর্ণনা করার সময় সম্ভবত এমন কিছুই বুঝিয়েছেন সিদ্ধার্থ। তাঁর বাবার বাড়ি মোটেই নোংরা ছিল না, কিন্তু তাঁর হৃদয়ে টান সৃষ্টিকারী মানুষে ও তাঁর চোখে মূল্যবান জিনিসপত্রে ছিল পরিপূর্ণ ছিল। পবিত্রতায় বসবাস করতে চাইলে তাঁকে এইসব বাঁধন ছিন্ন করে মুক্ত হতেই হবে। একেবারে গোড়া থেকেই সিদ্ধার্থ গৌতম ধরে নিয়েছিলেন সাংসারিক জীবন আধ্যাত্মিকতার সর্বোচ্চ পর্যায়ের সঙ্গে মানানসই নয়। এটা কেবল ভারতের অন্যান্য সাধুদের ধারণা ছিল না, বরং জেসাসও এমনটাই মনে করতেন। পরবর্তীকালে তিনি শিষ্যদের বলেছেন তাঁকে অনুসরণ করতে চাইলে অবশ্যই স্ত্রী-সন্তান ত্যাগ করতে হবে; পরিত্যাগ করতে হবে বয়োজ্যেষ্ঠ আত্মীয়দের।[৬]
সুতরাং আমাদের চলতি ‘পারিবারিক মূল্যবোধের’ বিশ্বাসের সঙ্গে একমত হতেন না গৌতম। পৃথিবীর অন্যান্য অংশে কুনফুসিয়াস (৫৫১-৪৭১) এবং সক্রেটিসের মতো তাঁর সমসাময়িক বা প্রায় সমসাময়িক ব্যক্তিরাও তাই। অবশ্যই সংসারি ছিলেন না তাঁরা, কিন্তু এই সময়কালে মানুষের দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রধান ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। কেন এই প্রত্যাখ্যানের প্রবণতা? পরবর্তী সময়ের বুদ্ধ ধর্মগ্রন্থসমূহ গৌতমের সংসার ত্যাগ ও তাঁর গৃহহীনতার পথে ‘অগ্রসর হওয়ার’ বিস্তারিত পৌরাণিক বিবরণ গড়ে তুলবে। বর্তমান অধ্যায়ের শেষ দিকে আমরা সেসব বিবেচনা করব। কিন্তু পালি লিপির প্রথম দিকের টেক্সটসমূহ তরুণের সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ বর্ণনা তুলে ধরে। মানুষের জীবনের দিকে তাকিয়ে গৌতম কেবলই দুঃখ-কষ্টের এক করুণ চক্র দেখতে পেয়েছেন। জন্ম-যন্ত্রণা দিয়ে যার শুরু এবং যা অনিবার্যভাবে ‘জরা, অসুস্থতা, মৃত্যু, বিষাদ ও বিকৃতির’[৭] দিকে এগিয়ে যায়। এই সর্বজনীন নিয়মের কোনও ব্যতিক্রম নন তিনি। এখন তিনি তরুণ, স্বাস্থ্যবান এবং সুদর্শন, কিন্তু যখনই আসন্ন ক্লেশের কথা ভাবতে যান, তারুণ্যের সমস্ত আনন্দ ও আস্থা তাঁকে ছেড়ে যায়। বিলাসী জীবনযাত্ৰা অর্থহীন, তুচ্ছ মনে হয়। জরাগ্রস্ত কোনও বৃদ্ধ পুরুষ বা ঘৃণ্য কোনও রোগে বিকৃত হয়ে যাওয়া কাউকে দেখে ‘বিদ্রোহী’ হয়ে ওঠার অনুভূতি মানিয়ে উঠতে পারেন না। একই নিয়তি–কিংবা এর চেয়ে খারাপ কিছু–তাঁর ও তাঁর প্রিয়জনের উপর পতিত হবে।[৮] তাঁর বাবা-মা, শিশু-পুত্রসহ স্ত্রী, বন্ধুবান্ধব সবাই সমান নাজুক ও দুর্বল। ওদের আঁকড়ে ধরে ভালোবাসায় আকৃষ্ট হওয়ার সময় আবেগের সাথে এমন কিছুতে নিজেকে জড়াচ্ছেন যা কেবল দুঃখ বয়ে আনতে পারে। স্ত্রী সৌন্দর্য হারাবে, ছোট্ট রাহুলা আগামীকালই মারা যেতে পারে। মরণশীল, ক্ষণস্থায়ী বস্তুর মাঝে সুখের সন্ধান কেবল অযৌক্তিকই নয়: ভালোবাসার পাত্র ও নিজের জন্যে অপেক্ষমান দুঃখ-দুর্দশা বর্তমানের ওপর গভীর ছায়া ফেলেছে, এইসব সম্পর্কের সমস্ত আনন্দ কেড়ে নিয়েছে।
কিন্তু জগতকে এমন বিবর্ণ রূপে কেন দেখেছেন গৌতম? মরণশীলতা জীবনের এমন এক সত্য যা সহ্য করা কঠিন। মানুষই একমাত্র প্রাণী যারা একদিন মারা যেতে হবে জেনে জীবন ধারণ করে। বিলুপ্তির এই দর্শন নিয়ে চিন্তা করা সব সময়ই তার কাছে কঠিন ঠেকে। কেউ কেউ স্রেফ বালিতে মাথা লুকিয়ে জগতের দুঃখের কথা ভাবতে অস্বীকার যায়। কিন্তু এটা অবশ্যই সঠিক নয়, কারণ আমরা পুরোপুরি অপ্রস্তুত অবস্থায় থাকলে জীবনের ট্র্যাজিডি বিপর্যয়কর হয়ে দাঁড়াতে পারে। প্রাচীন কাল থেকেই নারী-পুরুষ হতাশাব্যাঞ্জক ভিন্নরকম প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও আমাদের অস্তিত্বের পরম অর্থ ও মূল্য আছে এমন একটা বোধের চর্চা করার জন্যে ধর্মের উৎপত্তি ঘটিয়েছিল। কিন্তু মাঝে মাঝে বিশ্বাসের মিথ ও অনুশীলনকে অবিশ্বাস্য ঠেকে। মানুষ তখন নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের ক্লেশের ঊর্ধ্বে ওঠার জন্যে অন্য উপায়ের আশ্রয় নেয়: শিল্পকলা, সঙ্গীত, যৌনতা, খেলাধুলা কিংবা দর্শন। আমরা খুব সহজে হতাশ হয়ে পড়ি আবার আমরাই জীবন যে ভালো কিছু, নিজেদের মাঝে সেই আস্থা সৃষ্টিতে কঠোর পরিশ্রম করি, যদিও চারপাশে যন্ত্রণা, নিষ্ঠুরতা, অসুস্থতা আর অনাচারই দেখতে পাই কেবল। গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কেউ হয়তো ভাবতে পারে গৌতম বুদ্ধ জীবনের তিক্ত বাস্তবতার সঙ্গে মানিয়ে চলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলেন; পরিণত হয়েছিলেন এক গভীর বিষণ্নতার শিকার।
কিন্তু ব্যাপারটা তেমন ছিল না। এক সাধারণ ভারতীয় গৃহের সাংসারিক জীবন নিয়ে প্রকৃতই মোহমুক্তি ঘটেছিল গৌতমের, কিন্তু তিনি খোদ জীবনের আশা হারাননি। বরং সম্পূর্ণ উল্টো। তিনি স্থির নিশ্চিত ছিলেন, অস্তিত্বের হেঁয়ালির একটা সমাধান আছে, তিনিই সেটা উদ্ধার করতে পারবেন। গৌতম ‘পেরেলিয়ান দর্শন’ নামে পরিচিত দর্শনের অনুসারী ছিলেন, কারণ প্রাক- আধুনিক পৃথিবীর সকল সংস্কৃতির মানুষের কাছে তা সুবিদিত ছিল।[৯] ঐ জাগতিক জীবন অনিবার্যভাবে নাজুক এবং মৃত্যুর ছায়ায় এর অবস্থান, কিন্তু তা সমগ্ৰ বাস্তবতাকে তুলে ধরে না। ধারণা করা হতো মর্ত্য জীবনের সমস্ত কিছুর আরও শক্তিশালী, ইতিবাচক স্বর্গীয় অনুকৃতি রয়েছে। এখানে আমাদের সব অভিজ্ঞতাই স্বর্গীয় বলয়ের একটা আদি রূপের অনুসরণ: দেবতাদের জগৎ হচ্ছে আদি নকশা, মানবীয় বাস্তবতা যার মলিন ছায়ামাত্র। এই ধারণা প্রাচীন বিশ্বের বেশির ভাগ সংস্কৃতির মিথোলজি, আচার এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তুলে ধরে এবং আমাদের কালের অধিকতর প্রথাগত সমাজকে প্রভাবিত করে চলেছে। আধুনিক বিশ্বে আমাদের পক্ষে এমন ধারণা উপলব্ধি করা কঠিন, কারণ একে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় প্রমাণ করা যাবে না; আমরা যাকে সত্যের জন্যে অনিবার্য মনে করি সেই যৌক্তিক অবলম্বনের ঘাটতি রয়েছে এর। কিন্তু এই মিথ সত্যিই আমাদের অপরিণত বোধ তুলে ধরে যে, জীবন অসম্পূর্ণ এবং এখানেই সব কিছু শেষ হতে পারে না; নিশ্চয়ই অন্য কোথাও আরও ভালো, পূর্ণাঙ্গ ও সন্তুষ্টিকর একটা কিছু আছে। নিবিড় ও আন্তরিক প্রতীক্ষা শেষে প্রায়শঃ মনে হয় আমাদের ঠিক নাগালের বাইরে কিছু একটা রয়ে গেছে। গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্থক্যসহ এই বিশ্বাসের অংশীদার ছিলেন গৌতম। এই ‘একটা কিছু’ দেবতাদের স্বর্গীয় জগতে সীমাবদ্ধ, এটা বিশ্বাস করেননি তিনি। তাঁর বিশ্বাস ছিল, দুঃখ-দুর্দশা, শোক ও যন্ত্রণা-ভরা মরণশীল এই জগতেই তিনি একে প্রদর্শনযোগ্য বাস্তবতায় পরিণত করতে পারবেন।
এভাবে নিজেকে যুক্তি দেখিয়েছেন তিনি, আমাদের জীবনে ‘জন্ম, জরা, অসুস্থতা, মৃত্যু, দুঃখ আর দুর্নীতি’ থাকলে এইসব দুঃখ-দুর্দশার ইতিবাচক প্রতিরূপ থাকতেও বাধ্য; সুতরাং অস্তিত্বের আরেকটি ধরণ আছে। সেটা আবিষ্কার করাই তাঁর কাজ। ‘ধরা যাক,’ বলেছেন তিনি, ‘আমি যদি অজাত, অজর, অসুখহীন, মৃত্যুহীন, দুঃখহীন, অবিকৃত ও এই বন্ধন হতে পরম মুক্তির সন্ধান শুরু করি?’ পরিপূর্ণ সন্তুষ্টিকর এই অবস্থাকে তিনি বললেন নিব্বানা (‘নির্বাপিত হওয়া’)।[১০] গৌতমের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, আমরা যেভাবে ফুঁ দিয়ে অগ্নিশিখা নিভিয়ে দিই ঠিক তেমনি মানবাত্মার এত দুঃখ-কষ্টের কারণ আবেগ, সম্পর্ক ও মোহকে ‘নির্বাপিত’ করা সম্ভব। নিব্বানা লাভ অনেকটা আমরা জ্বর হতে সেরে ওঠার পর যেমন ‘ঠাণ্ডা’ অনুভব করি অনেকটা সেকরম: গৌতমের আমলে সম্পর্কিত বিশেষণ নিব্বুতা দৈনন্দিন খিঁচুনি বোঝাতে ব্যবহৃত শব্দ ছিল। তো গৌতম গৃহত্যাগ করছিলেন মানুষকে আক্রান্তকারী অসুস্থতার একটা প্রতিকারের খোঁজে যা নারী ও পুরুষকে অসুখে পূর্ণ করে রাখে। জীবনকে এমন হতাশাব্যঞ্জক ও দুঃসহ করে তোলা এই সর্বজনীন দুঃখদুর্দশা চিরকাল বয়ে বেড়ানো আমাদের নিয়তি নয়। আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতা বর্তমানে ভ্রান্তিময় হলেও, আদিরূপের আইন অনুযায়ী অস্তিত্বের আরেকটা রূপ নিশ্চয়ই আছে যা ত্রুটিপূর্ণ ও ক্ষণস্থায়ী নয়। ‘এমন কিছু আছে যা সাধারণভাবে জন্ম নেয় না, যেটা সৃষ্টও নয় আবার যা অক্ষত থেকে যায়,’ পরবর্তী জীবনে জোর দিয়ে বলবেন গৌতম। ‘এর অস্তিত্ব না থাকলে, উদ্ধার পাওয়ার উপায় বের করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।’[১১]
আধুনিক কেউ তাঁর এমনি আনাড়ি আশাবাদে হাসতে পারেন, চিরকালীন আদিরূপের মিথকে সম্পূর্ণ আজগুবি মনে করতে পারেন। কিন্তু গৌতম দাবি করেছেন, উদ্ধারের পথ পেয়েছেন তিনি, সুতরাং নিব্বানার অস্তিত্ব ছিল। অবশ্য বহু ধর্মীয় ব্যক্তির মতো তিনি এই মহৌষধকে অতিপ্রাকৃত মনে করেননি। অন্য জগৎ হতে স্বর্গীয় সহায়তার ওপর নির্ভর করেননি তিনি। বরং তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল, নিব্বানা এমন একটা অবস্থা যা মানব সন্তানের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। যে কোনও প্রকৃত সন্ধানীই এর দেখা পাবে। গৌতম বিশ্বাস করেছেন এই অসম্পূর্ণ জগতেই তিনি তাঁর কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা পাবেন। দেবতাদের বার্তার অপেক্ষায় না থেকে উত্তরের খোঁজে নিজের মাঝে সন্ধান চালাবেন, মনের দূরতম কন্দরে ঢুকবেন এবং তাঁর সকল শারীরিক সম্পদ কাজে লাগাবেন। শিষ্যদের একই কাজ করতে বলবেন তিনি। জোর দিয়ে বলবেন, কেউ যেন তাঁর শিক্ষাকে জনশ্রুতি ধরে না নেয়। তাদের অবশ্যই নিজস্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে তাঁর সমাধানের সত্যতা প্রমাণ করতে হবে। নিজেদেরই বের করতে হবে যে, তাঁর পদ্ধতি ফল দেয়। দেবতাদের কাছ থেকে কোনও সাহায্য প্রত্যাশা করতে পারবে না তারা। দেবতাদের অস্তিত্ব আছে, বিশ্বাস করতেন গৌতম, কিন্তু তাঁদের ব্যাপারে তেমন আগ্রহী ছিলেন না। এখানেও তাঁর সময় ও সংস্কৃতিরই মানুষ ছিলেন তিনি। ভারতীয় জনগণ অতীতে দেবতাদের পূজা করেছে: বনদেবতা ইন্দ্র; স্বর্গীয় শৃঙ্খলার রক্ষক বরুণ; অগ্নিদেবতা অগ্নি। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দী নাগাদ এইসব দেবতা অধিকাংশ চিন্তাশীল মানুষের ধর্মীয় সচেতনতা থেকে হারিয়ে যেতে শুরু করেছিলেন। তাদেরকে ঠিক মূল্যহীন হিসাবে দেখা হতো না, কিন্তু পূজা-অর্চনার পাত্র হিসাবে অপর্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন। মানুষ ক্রমবর্ধমান হারে সচেতন হয়ে উঠছিল যে, দেবতারা তাদের প্রকৃত ও যথার্থ সাহায্য করতে পারবেন না। তাঁদের সম্মানে প্রদত্ত উৎসর্গ আসলে মানবীয় দুর্দশা প্রশমিত করেনি। অধিক হারে নারী-পুরুষ পুরোপুরি নিজেদের ওপর নির্ভর করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল। তাদের বিশ্বাস ছিল সৃষ্টি জগৎ নৈর্ব্যক্তিক আইনে শাসিত হয়, দেবতারাও যার অধীন। দেবতারা গৌতমকে নিব্বানার পথ দেখাতে পারবেন না, তাঁকে আপন প্রয়াসের ওপর নির্ভর করতে হবে।
সুতরাং নিব্বানা ক্রিশ্চানদের স্বর্গের মতো কোনও জায়গা নয় যেখানে মৃত্যুর পর বিশ্বাসীরা দল বেঁধে যাবে। প্রাচীন বিশ্বের খুবই অল্প সংখ্যক মানুষ এই পর্যায়ে আনন্দময় অমরত্বের আশা করত। প্রকৃতপক্ষে, গৌতমের আমলে ভারতীয় জনগণ বর্তমান যন্ত্রণাকর অস্তিত্বের নিগড়ে পুরোপুরি বন্দি মনে করছে নিজেদের। ষষ্ঠ শতাব্দীতে ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা লাভকারী পুনর্জন্মের মতবাদ থেকে যেমনটা দেখতে পাই আমরা। মনে করা হতো যে, নারী বা পুরুষ মৃত্যুর পর তার বর্তমান জীবনের কর্মকাণ্ডের (কম্ম) মান দিয়ে নির্ধারিত এক নতুন রূপে পুনর্জন্ম নেবে। খারাপ কৰ্ম্ম’র মানে হবে আপনি ক্রীতদাস, জানোয়ার বা গাছ হিসাবে পুনর্জন্ম নেবেন; সুকৰ্ম্ম পরবর্তী কালে উন্নত অস্তিত্ব নিশ্চিত করবে: আপনি রাজা এমনকি দেবতা হিসাবেও পুনর্জন্ম লাভ করতে পারেন। কারণ কোনও একটি স্বর্গে পুনর্জন্ম লাভ করা সুখকর পরিসমাপ্তি নয়, কারণ ঐশ্বরিকতা অন্য যে কোনও অবস্থার চেয়ে অধিকতর স্থায়ী নয়। শেষ পর্যন্ত এমনকি দেবতারও তাঁকে স্বর্গীয় রূপ দানকারী সৎ কম্ম ফুরিয়ে যাবে, তিনি মারা যাবেন এবং পৃথিবীতে কম সুবিধাজনক অবস্থায় পুনর্জন্ম নেবেন। সুতরাং, সকল সত্তাই সামসারা (‘এগিয়ে নেওয়া’)র অন্তহীন চক্রে বাঁধা পড়ে আছে যা তাকে এক জীবন থেকে অন্য জীবনে ঠেলে দেয়। বহিরাগত কারও কাছে একে উদ্ভট তত্ত্ব মনে হয়, কিন্তু এটা দুঃখ-দুর্দশার সমস্যা সমাধানের সিরিয়াস প্রয়াস ছিল। একে প্রায়শঃই দুষ্টের পালনকারী ও ঘনঘন ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বলে মনে হওয়া ব্যক্তিরূপী ঈশ্বরকে মানুষের নিয়তি নির্ধারণের জন্যে দায়ী করার চেয়ে অন্তস্থভাবে অনেক বেশি সন্তোষজনক হিসাবে দেখা যেতে পারে। কম্মের বিধান সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক মেকানিজম যা ন্যায়সঙ্গতভাবে কারও প্রতি বৈষম্য ছাড়াই প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু একের পর এক জীবন কাটানোর সম্ভাবনা উত্তর ভারতের অধিকাংশ মানুষের মতো গৌতমকেও আতঙ্কে পূর্ণ করে তুলেছিল।
এটা হয়তো বোঝা কঠিন। আজকাল আমাদের অনেকেই অনুভব করেন যে আমাদের জীবন অতি সংক্ষিপ্ত। নতুন করে জীবন শুরুর সুযোগ পেলে তাঁরা খুশি হবেন। কিন্তু গৌতম ও তাঁর সমসাময়িকদের পুনঃমৃত্যুর চেয়ে পুনর্জন্মের সম্ভাবনাই বেশি আতঙ্কের কারণ ছিল। জরাগ্রস্থ হওয়ার প্রক্রিয়া সহ্য করা বা ক্রমাগত অসুস্থ হতে হতে ভীতিকর ও যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর মোকাবিলা একবারই যথেষ্ট খারাপ ছিল, কিন্তু বারবার এই প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে যেতে বাধ্য হওয়াটা অসহনীয়, একেবারেই অর্থহীন মনে হয়েছে। মানুষকে সামসারা থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করে চূড়ান্ত মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যেই সে সময়ের অধিকাংশ ধর্মীয় সমাধান পরিকল্পিত হয়েছিল। নিব্বানার মুক্তি ছিল বোধের অতীত, কারণ তা আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা হতে বহু দূরবর্তী ছিল। হতাশা, দুঃখ বা বেদনা নেই, আবার আমাদের নিয়ন্ত্রণের অতীত উপাদানে বাঁধা নয় এমন একটা জীবনধারা বর্ণনা করার বা চিন্তা করার মতো কোনও ভাষা নেই আমাদের। কিন্তু গৌতমের আমলের সাধুরা এই স্বাধীনতাকে প্রকৃত সম্ভাবনা বলে মেনে নিয়েছিলেন। পশ্চিমা জনগণ প্রায়ই ভারতীয় চিন্তাচেতনাকে নেতিবাচক ও নাস্তিবাদী বলে বর্ণনা করে থাকে। আসলে তা নয়। এটা ছিল শ্বাসরুদ্ধকরভাবে আশাবাদী। গৌতম পরিপূর্ণভাবে এর অংশীদার ছিলেন।
খাবারের জন্যে হাত পাতে এমন একজন যাযাবর সন্ন্যাসীর গেরুয়া বসন পরে গৌতম যখন পিতৃগৃহ ত্যাগ করলেন, তাঁর বিশ্বাস ছিল উত্তেজনাকর কোনও অ্যাডভেঞ্চার নেমেছেন তিনি। তিনি ‘প্রশন্ত পথে’র প্রলোভন ও ‘গৃহহীনতা’র উজ্জ্বল, নিখুঁত অবস্থা অনুভব করেছেন। এই সময় সকলেই ‘পবিত্র জীবন’কে মহান অনুসন্ধান বলে উল্লেখ করত। রাজা, বণিক ও সম্পদশালী পরিবারগুলো সমানভাবে এই ভিক্ষুদের সম্মান করত, তাদের খাওয়ানোর সুযোগ পেতে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামত। কেউ কেউ তাদের নিয়মিত পৃষ্ঠপোষক ও শিষ্যে পরিণত হয়েছিল। এটা কোনও উন্মাদনা ছিল না। ভারতীয় জনগণ অন্য যে কারও মতো বস্তুবাদী হতে পারে, কিন্তু আধ্যাত্মিকতা সন্ধানকারীদের সম্মান দেখানোর সুপ্রাচীন ঐতিহ্য রয়েছে তাদের। তারা তাদের সমর্থন অব্যাহত রেখেছে। তারপরও বিসিই ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিকে গাঙ্গেয় এলাকায় বিশেষ একরকম তাগিদ ছিল। মানুষ গৃহত্যাগীদের দুর্বল সমাজ-ত্যাগী হিসাবে দেখেনি। ওই অঞ্চলে আধ্যাত্মিক সংঘাত চলছিল। গৌতমের অনুভূত বিভ্রান্তি ও বৈষম্যের ব্যাপকতা ছিল। সাধারণ মানুষ একটা নতুন ধর্মের প্রয়োজন সম্পর্কে মরিয়াভাবে সচেতন ছিল। এভাবে সন্ন্যাসী এমন এক অনুসন্ধানে লিপ্ত ছিলেন যা প্রায়শঃই নিজস্ব বিশাল ক্ষতির মাধ্যমে শিষ্যদের উপকারে আসবে। শক্তি, বল ও দক্ষতা বোঝাতে গৌতমকে প্রায়শঃই বীরত্বসূচক উপমায় বর্ণনা করা হয়। তাঁকে সিংহ, বাঘ ও হিংস্র হাতির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। তরুণ বয়সে তাঁকে ‘সুদর্শন অভিজাতজন, দুর্ধর্ষ সেনাদলের নেতা বা হস্তি বাহিনীর প্রধান’[১২] হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে। এই সন্ন্যাসীদের লোকে নারী-পুরুষকে দুঃখদুর্দশা থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে আত্মার জগতে অভিযান চালানো অগ্রগামী হিসাবে দেখত। চলমান অস্থিরতার কারণে অনেকেই একজন বুদ্ধের আগমন আকাঙ্ক্ষা করত, এমন একজন যিনি ‘আলোকপ্রাপ্ত,’ মানুষের পূর্ণ সম্ভাবনায় ‘জাগ্রত’। যিনি আকস্মিকভাবে অচেনা ও নিঃসঙ্গ হয়ে ওঠা এক জগতে শান্তির খোঁজ পেতে অন্যদের সাহায্য করতে পারবেন।
ভারতের জনগণ কেন জীবন সম্পর্কে এমন অস্বস্তিকর অনুভূতি লাভ করেছিল? এই অস্থিরতা কেবল উপ-মহাদেশেই সীমিত ছিল না, বরং সভ্য জগতের বেশ কিছু দূরবর্তী অঞ্চলের মানুষকেও আক্রান্ত করেছিল। ক্রমবর্ধমান সংখ্যকের ধারণা জন্মেছিল যে, তাদের পূর্বসুরিদের অনুসৃত আধ্যাত্মিক অনুশীলন আর কাজে আসছে না। দার্শনিক ও ভাববাদী প্রতিভাবানরা সমাধান বের করার জন্যে ব্যাপক প্রয়াস পেয়েছিলেন। কোনও কোনও ইতিহাসবিদ মানবজাতির জন্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বলে এই সময়কালকে (৮০০ থেকে ২০০ বিসিই পর্যন্ত বিস্তৃত) ‘অ্যাক্সিয়াল যুগ’ বলে অভিহিত করেন। এই সময়ে বিকশিত সামাজিক মূল্যবোধ বর্তমান কালেও নারী-পুরুষকে পরিপুষ্ট করে চলেছে।[১৩] অষ্টম, সপ্তম ও ষষ্ঠ শতকের মহান হিব্রু পয়গম্বর, ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতাব্দীতে চীনের ধর্মীয় ঐতিহ্যের সংস্কার সাধনকারী কনফুসিয়াস ও লাও সু; ষষ্ঠ শতকের ইরানি সাধু যরোস্ট্রার; এবং গ্রিকদের স্বয়ং-প্রমাণিত সত্য বলে মনে হওয়া বিষয়গুলোকে প্রশ্ন করতে উদ্বুদ্ধকারী সক্রেটিস ও প্লেটোর (৪২৭-৩২৭) পাশপাশি অ্যাক্সিয়াল যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নক্ষত্রে পরিণত হবেন গৌতম। এই ব্যাপক পরিবর্তনে অংশগ্রহণকারীরা এক নয়া জমানার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হয়েছেন, তাঁরা কোনও কিছুই আর আগের মতো থাকবে না বলে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন।
অ্যাক্সিয়াল যুগ বর্তমানে আমাদের পরিচিত মানব জাতির সূচনা নির্দেশ করে। এই সময়কালে নারী-পুরুষ তাদের অস্তিত্ব, আপন প্রকৃতি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে নজীরবিহীনভাবে সচেতন হয়ে উঠেছিল।[১৪] এক নিষ্ঠুর জগতে নিজেদের প্রবল অক্ষমতার অনুভূতি আপন সত্তার মাঝে সর্বোচ্চ লক্ষ্য ও পরম সত্যি সন্ধানে বাধ্য করেছে তাদের। সময়ের মহান সাধুরা মানুষকে জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো, নিজেদের দুর্বলতার ঊর্ধ্বে ওঠার কৌশল ও ত্রুটিপূর্ণ জগতে শান্তিতে বসবাস করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। এই সময়ে গড়ে ওঠা নতুন ধর্মীয় ব্যবস্থাগুলো–চীনে তাওবাদ ও কুনফুসিয়াবাদ, ভারতে বুদ্ধ মতবাদ ও হিন্দু মতবাদ, ইরান ও মধ্যপ্রাচ্যের একেশ্বরবাদ, ইউরোপের গ্রিক যুক্তিবাদ–সুস্পষ্ট পার্থক্য সত্ত্বেও মৌলিক কিছু বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। কেবল এই ব্যাপক পরিবর্তনে যোগ দিয়েই বিশ্বের বিভিন্ন জাতি অগ্রগতি অর্জন ও ইতিহাসের অগ্রযাত্রায় শরিক হতে পেরেছিল।[১৫] কিন্তু এর ব্যাপক গুরুত্ব সত্ত্বেও অ্যাক্সিয়াল যুগ রহস্যময় রয়ে গেছে। মাত্র তিনটি প্রধান এলাকায়–চীন, ভারত ও ইরানে–আর পূর্ব ভূমধ্য মহাসাগরীয় এলাকায় তা শেকড় গেড়েছিল কেন কেউ জানে না, আমরা এর উদ্ভবের কারণও জানি না। কেন কেবল চীনা, ইরানি, ভারতীয়, ইহুদি ও গ্রিকরা এই নতুন দিগন্তের অভিজ্ঞতা পেয়েছিল এবং আলোকন ও মুক্তির নতুন এই অনুসন্ধান যোগ দিয়েছিল? বাবিলনবাসী ও মিশরিয়রাও মহান সভ্যতা গড়ে তুলেছিল, কিন্তু এই পরিচয়ে তারা অ্যাক্সিয়াল আদর্শ গড়ে তোলেনি। বেশ পরে নতুন মল্যবোধে যোগ দিয়েছে: অ্যাক্সিয়াল প্রবণতার পুনরাবৃত্তি ইসলাম বা ক্রিশ্চান ধর্মে। কিন্তু অ্যাক্সিয়াল দেশগুলোয় অল্প সংখ্যক মানুষ নতুন সম্ভাবনার আভাস পেয়ে প্রাচীন প্রথা ভেঙে বেরিয়ে গেছে। তারা তাদের সত্তার গভীর কন্দরে পরিবর্তন সন্ধান করেছে, আধ্যাত্মিক জীবনে বৃহত্তর অন্তর্মুখীতা চেয়েছে আর স্বাভাবিক জাগতিক অবস্থা ও রীতির ঊর্ধ্বে এক বাস্তবতার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার প্রয়াস পেয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এই কালপর্বের পর মনে করা হয়েছে যে, কেবল তাদের সীমার বাইরে পৌঁছানোর ভেতর দিয়ে মানব সন্তান পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারবে।
লিখিত ইতিহাসের সূচনা কেবল বিসিই ৩০০ শতাব্দীর দিকে। তার আগে পর্যন্ত মানুষ কীভাবে জীবন কাটাত, সমাজ সংগঠিত করত তার সামান্যই লিপিবদ্ধ দলিল রয়েছে আমাদের হাতে। কিন্তু মানুষ বরাবরই প্রাগৈতিহাসিক ২০,০০০ বছর কেমন ছিল কল্পনা করতে চেয়েছে। নিজেদের অভিজ্ঞতা আবাদ করতে চেয়েছে সেখানে। গোটা বিশ্বে, প্রতিটি সংস্কৃতির মিথোলজিতে এই প্রাচীন কালগুলো বর্ণিত হয়েছে, এগুলোর কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই, কিন্তু স্বর্গ ও আদি বিপর্যয়ের কথা বলে এগুলো।[১৬] স্বর্ণযুগে, বলা হয়, দেবতারা মর্ত্যে মানুষের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছেন। বুক অভ জেনেসিসে বর্ণিত পশ্চিমের হারানো স্বর্গ গার্ডেন অভ ইডেনের কাহিনী তো টিপিক্যাল: কোনও এক কালে মানুষ ও স্বর্গের মাঝে কোনও বিভেদ ছিল না: সন্ধ্যার শীতল পরিবেশে উদ্যানে ঘুরে বেড়াতেন ঈশ্বর। মানুষ পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন ছিল না। আদম ও ইভ তাঁদের যৌনতা বা ভালো মন্দের পার্থক্য সম্পর্কে কিছু না জেনেই শান্তিতে বাস করতেন। আমাদের অধিকতর বিচ্ছিন্ন জীবনে এমন ঐক্য কল্পনা করা অসম্ভব। কিন্তু প্রায় সব সংস্কৃতিতেই এই আদি একতার মিথ দেখিয়েছে যে, মানবজাতি মানুষের জন্যে যথাযথ অবস্থা হিসাবে অনুভূত এক ধরনের শান্তি ও সমগ্রতার আকাঙ্ক্ষা অব্যাহত রেখেছে। আত্মসচেতনতার উন্মেষকে স্বর্গ হতে কষ্টকর পতন হিসাবে প্রত্যক্ষ করেছে তারা। হিব্রু বাইবেল এই সমগ্রতা ও সম্পূর্ণতাকে শালোম বলে: গৌতম নিব্বানার কথা বলে তার সন্ধানে গৃহ ছেড়েছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষ অতীতে শান্তি ও পূর্ণতায় বসবাস করেছে, কিন্তু সে পথ বিস্মৃত হয়েছে তারা।
আমরা যেমন দেখেছি, গৌতম নিজের জীবন অর্থহীন ভেবেছেন। অ্যাক্সিয়াল দেশসমূহে আবির্ভূত আধ্যাত্মিকতার মৌল বিষয় ছিল জগতের কুটিলতা। এই পরিবর্তনে অংশগ্রহণকারীরা ঠিক গৌতমের মতো অস্থিরতা বোধ করেছে। অসহায়ত্বের একটা অনুভূতিতে আক্রান্ত হয়েছে তারা, মরণশীলতার কারণে বিকারগ্রস্থ হয়ে গভীর আতঙ্কে জগৎ হতে বিচ্ছিন্ন বোধ করেছে।[১৮] বিভিন্নভাবে এই অস্থিরতা প্রকাশ করেছে তারা। গ্রিকরা জীবনকে ট্র্যাজিক মহাকাব্য হিসাবে দেখেছে, এমন এক নাটক যেখানে তারা ক্যাথারসিস ও মুক্তির সংগ্রাম করেছে। প্লেটো স্বর্গ হতে মানুষের বিচ্ছিন্নতার কথা বলেছেন ও আমাদের বর্তমান অবস্থার ত্রুটি দূর করে শুভের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেছেন। অষ্টম, সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর হিব্রু পয়গম্বরগণ ঈশ্বর হতে একই ধরনের দূরত্ব অনুভব করেছেন; তাঁদের রাজনৈতিক নির্বাসনকে আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রতীক মনে করেছেন। ইরানের যোরাস্ট্রারবাদীরা জীবনকে শুভ ও অশুভের সংঘাত হিসাবে দেখেছে; অন্যদিকে চীনে কনফুষিয়াস তাঁর দেশের পূর্বসুরিদের আদর্শ হতে বিচ্যুত হওয়ায় অন্ধকার কাল নেমে আসায় বিলাপ করেছেন। ভারতে গৌতম ও বনবাসী সন্ন্যাসীদের বিশ্বাস জেগেছিল যে, জীবন একটা দুঃখ; মূলত ‘কুটিল,’ যন্ত্রণা, দুঃখ ও বিষাদে পূর্ণ। পৃথিবী এক আতঙ্কময় স্থানে পরিণত হয়েছে। বুদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ লোকে শহর ছেড়ে বনে যাবার পরবর্তী অভিজ্ঞতাকে ‘আতঙ্ক, ভয় ও শঙ্কা’র বলে উল্লেখ করেছে।’[১৯] প্রকৃতি হয়ে পড়েছিল দুর্বোধ্যরকম ভীতিকর, অনেকটা যেমন আদাম ও ইভের অপরাধ সংঘটনের পর প্রতিকূল হয়ে গিয়েছিল। বুনো প্রকৃতির সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তুলবেন বলে গৃহ ত্যাগ করেননি গৌতম; লাগাতার ‘আতঙ্ক ও শঙ্কা’[২০] বোধ করেছেন তিনি। কাছেপিঠে কোনও হরিণ এলে বা হাওয়ায় পাতা দুলে উঠলেও, পরে স্মৃতিচারণ করেছেন তিনি, চুল খাড়া হয়ে যেত তাঁর।
কী ঘটেছিল? অ্যাক্সিয়াল যুগের আধ্যাত্মিকতাকে ইন্ধন যোগানো বিষাদকে কেউই পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করেননি। নিঃসন্দেহে নারী-পুরুষ আগেও কষ্ট ভোগ করেছে। আসলে এই সময়ের শত শত বছর আগের মিশর ও মেসোপটেমিয়ায় পাওয়া প্রস্তরলিপিতে একইরকম মোহমুক্তির প্রকাশ ঘটেছে। কিন্তু তিনটি মূল অ্যাক্সিয়াল অঞ্চলে কেন দুঃখ-কষ্টের অভিজ্ঞতা এমন উত্তুঙ্গে পৌঁছেছিল? কোনও কোনও ইতিহাসবিদ এসব এলাকায় ইন্দো-ইউরোপিয় যাযাবর অশ্বারোহী বাহিনীর আগ্রাসনকে সাধারণ উপাদান মনে করেন। তৃতীয় সহস্রাব্দের শেষ নাগাদ এই আর্য গোত্রগুলো মধ্য এশিয়া ছেড়ে ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলে পৌঁছে যায়। এরা বিসিই ১২০০ নাগাদ ভারত ও ইরানে থিতু হয়েছিল; দ্বিতীয় সহস্রাব্দ নাগাদ থিতু হয়েছিল চীনে। সঙ্গে করে বিশাল দিগন্ত ও অমিত সম্ভাবনার বোধ নিয়ে এসেছিল তারা। উন্নত জাতি হিসাবে এক করুণ রসের মহাকাব্যিক সচেতনতাবোধ গড়ে তুলেছিল। প্রাচীন আস্তাবল ও অধিকতর আদিম সমাজকে তারা প্রতিস্থাপিত করেছিল তবে সেটা কেবল প্রবল বিদ্বেষ আর বিপর্যয়ের কাল অতিক্রমের পরেই, যা অ্যাক্সিয়াল যুগের অস্থিরতার কারণ হতে পারে।[২১] কিন্তু ইহুদি ও তাদের পয়গম্বরদের এইসব আর্য অশ্বারোহীর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ ছিল না। হাজার বছর ধরে এই আগ্রাসনগুলো পরিচালিত হয়েছে, অথচ প্রধান অ্যাক্সিয়াল পরিবর্তনগুলো লক্ষণীয়ভাবে সমকালীন ছিল।
এছাড়াও, উদাহরণ স্বরূপ, ভারতে গড়ে ওঠা আর্যদের সংস্কৃতির সঙ্গে অ্যাক্সিয়াল যুগের কোনও মিল ছিল না। বিসিই ১,০০০ সাল নাগাদ আর্য গোত্রগুলো থিতু হয়ে উপমহাদেশের বেশিরভাগ এলাকাতেই সমাজ গড়ে তুলেছিল। ভারতীয় সমাজকে এমনভাবে তারা দমিত করেছিল যে এখন আর আমরা সিন্ধু উপত্যকার দেশীয় প্রাক-আর্য লোকজন সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানতে পারি না। উৎসের গতিশীলতা সত্ত্বেও আর্য ভারত অ্যাক্সিয়াল-পূর্ব অধিকাংশ সংস্কৃতির মতো স্থবির ও রক্ষণশীল ছিল। সাধারণ মানুষকে সামন্ত বাদী ইউরোপে পরবর্তীকালে বিকশিত চারটি এস্টেটের অনুরূপ চারটি সুনির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করেছিল তা: ব্রাহ্মণরা ছিলেন পুরোহিত গোষ্ঠী, কাল্টের দায়িত্ব ছিল তাঁদের: সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা; ক্ষত্রিয় যোদ্ধারা সরকার ও প্রতিরক্ষায় নিযোজিত ছিল; বৈশ্যরা ছিল কৃষিজীবী ও পশু পালনকারী, যারা অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখত; এবং সুদ্ররা ছিল দাস বা অস্পৃশ্য, আর্য ব্যবস্থায় মিশে যেতে অক্ষম ছিল তারা। গোড়াতে চারটি শ্রেণী উত্তরাধিকারীমূলক ছিল না। প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকলে দেশীয় ভারতীয়রা ক্ষত্রিয় রা ব্রাহ্মণ হতে পারত। কিন্তু গৌতমের সময় আসতে আসতে সমাজের স্তর বিন্যাস পবিত্র তাৎপর্য অর্জন করে, হয়ে ওঠে অপরিবর্তনীয়; কেননা একে সৃষ্টির আদি আদর্শ জগতের প্রতিবিম্ব মনে করা হতো।[২২] এক গোত্র হতে আরেক গোত্রে গিয়ে এই শৃঙ্খলা পরিবর্তনের কোনও সুযোগ ছিল না।
আর্য আধ্যাত্মিকতা স্থিতাবস্থা মেনে নেওয়ার ওপর নির্ভরশীল প্রাচীন, অ্যাক্সিয়াল যুগ পূর্ববর্তী ধর্মগুলোর মতোই ছিল, জীবনের অর্থ নিয়ে আঁচ অনুমানের স্থান তেমন একটা ছিল না। পবিত্র সত্যকে সুনির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় হিসাবে দেখেছে; অনুসন্ধান না করে বরং নিষ্ক্রিয়ভাবে গ্রহণ করা হতো তাকে। আর্যরা সোমা নামে মাদক চাষ করত। ব্রাহ্মণদের পরমানন্দময় ঘোরে পৌঁছে দিত তা, ওই অবস্থায় বেদ নামে পরিচিত অনুপ্রেরণাজাত সংস্কৃত টেক্সট ‘শুনতেন’ (শ্রুতি) তাঁরা।[২৩] এসব দেবতাদের মুখ নিঃসৃত মনে করা হতো না, বরং চিরন্তভাবে অস্তিত্বশীল ও সৃষ্টির মৌল নীতিমালার প্রতিফলন বলে ধারণা করা হতো। দেবতা ও মানব জীবনকে সমানভাবে পরিচালনাকারী একটি সর্বজনীন বিধিও প্রাচীন ধর্মগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। উপমহাদেশে লেখার প্রচলন না থাকায় বেদ লিখা হয়নি। ফলে ব্রাহ্মণদের দায়িত্ব ছিল এইসব চিরন্তন সত্য মুখস্থ করে প্রজন্ম পরম্পরায় সংরক্ষণ করা। উত্তরাধিকারের এই কাহিনী বাবা হতে পুত্রকে দান করা হতো, যেহেতু এই পবিত্র জ্ঞান মানুষকে জগৎকে পবিত্র করে তোলা ও টিকে থাকতে সক্ষম করা মৌল নীতি ব্রহ্মার সংস্পর্শে পৌঁছে দিত। শত শত বছরের পরিক্রমায় আদি আর্য গোত্রসমূহের ভাষা সংস্কৃত স্থানীয় কথ্য ভাষার কাছে হার মানে, ফলে তা ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য সবার কাছে দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে–প্রকৃতপক্ষে এটাই অনিবার্যভাবে ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা ও মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছিল। সমগ্র জগতের অস্তিত্ব বজায় রাখে যে বেদ সেখানে উল্লেখিত উৎসর্গের উপাচার কেবল তাঁরাই জানতেন।
বলা হয়ে থাকে যে, সময়ের সূচনায় একজন রহস্যময় স্রষ্টা এক আদি উৎসর্গ সম্পন্ন করেছিলেন যা দেবতা, মানুষ ও গোটা সৃষ্টি জগতকে অস্তিত্ব দিয়েছে। আদি এই উৎসর্গই ব্রাহ্মণদের পশু বলীর অদিরূপ যা তাঁদের জীবন ও মৃত্যুর উপর ক্ষমতা দিয়েছিল। এমনকি দেবতারাও এই উৎসর্গের ওপর নির্ভরশীল; আচার ঠিক মতো পালন করা না হলে তাঁরাও কষ্টের শিকার হবেন। সুতরাং সমগ্র জীবন এইসব আচারকে ঘিরে আবর্তিত ছিল। ব্রাহ্মণরা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে স্পষ্টই গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন, কিন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। রাজা ও অভিজাতজনেরা উৎসর্গের ব্যয়ভার মেটাতেন, বৈশ্যরা শিকার হিসাবে পশু পালন করত। বৈদিক ধর্মে আগুনের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। প্রকৃতির শক্তিসমূহের উপর মানুষের ক্ষমতাকে প্রতীকায়িত করত তা। ব্রাহ্মণরা মন্দিরে মন্দিরে সযত্নে তিনটি পবিত্র অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে রাখতেন। গৃহস্থরাও যার যার উনুনের প্রতি পারিবারিক আচারের ভেতর দিয়ে সম্মান দেখাত। প্রতি চান্দ্র মাসের এক চতুর্থাংশ (উপোসাথা) দিবসে পবিত্র আগুনের উদ্দেশ্যে বিশেষ অর্ঘ্য প্রদান করা হতো। উপোসাথার আগে ব্রাহ্মণ ও সাধারণ গৃহস্থরা একইভাবে উপবাস পালন করতেন, যৌনতা ও কাজকর্ম থেকে বিরত থাকতেন, রাতে সতর্ক পাহারা দিতেন উনুন। উপবাসথা নামে পরিচিত পবিত্রক্ষণ ছিল সেটা, যখন দেবতারা আগুনের ধারে গৃহস্থ ও পরিবারের ‘পাশে অবস্থান’ করতেন।[২৪]
এভাবে বৈদিক ধর্মবিশ্বাস অ্যাক্সিয়াল-পূর্ব যুগের ধর্মের মতোই ছিল। এর উন্নতি বা পরিবর্তন ঘটেনিঃ একটি আদি আদর্শ ধরনের অনুগামী ছিল তা, ভিন্ন কিছুর প্রত্যাশা করেনি। কিছু বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের উপর নির্ভরশীল ছিল এটি যেগুলো ফলাফলের দিক থেকে জাদুকরী ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে মহাবিশ্বকে নিয়ন্ত্রণকারী; অল্প কজনের জানা প্রাচীন নিগূঢ় উপকথা ভিত্তিক।[২৫] গভীরভাবে রক্ষণশীল এই আধ্যাত্মিকতা কালহীন ও অপরিবর্তনীয় বাস্তবতায় নিরাপত্তার সন্ধান করেছে। নতুন অ্যাক্সিয়াল যুগের সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল তা। স্রেফ সক্রেটিসের কথা চিন্তা করাই যথেষ্ট, যত মহামহীমই হয়ে থাকুক না কেন, কখনওই প্রচলিত নিশ্চয়তাকে চূড়ান্ত মেনে নেননি তিনি। শ্রুতি বেদের মতো বাইরে থেকে জ্ঞান আহরণের বদলে প্রত্যেকেরই আপন সত্তার গভীরে সত্যের সন্ধান করা উচিত বলে মনে করতেন তিনি। সমস্ত কিছুকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন সক্রেটিস। নিজস্ব বিভ্রান্তি দিয়ে আলোচনাকারীকে আক্রান্ত করতেন, কারণ বিভ্রান্তিই দার্শনিক অনুসন্ধানের সূচনা। হিব্রু পয়গম্বরগণ প্রাচীন ইসরায়েলের কিছু কিছু প্রাচীন পৌরাণিক নিশ্চয়তা উল্টে দিয়েছিলেন: ঈশ্বর আর আপনাআপনি মিশর থেকে যাত্রার সময়ের মতো মনোনীত জাতির সঙ্গে ছিলেন না। এবার তিনি জেন্টাইল জাতিগুলোকে ইহুদিদের শান্তি দেওয়ার জন্যে ব্যবহার করবেন, যাদের সবারই ন্যায় বিচার, সাম্য ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করার কথা ছিল। মুক্তি অর্জন ও টিকে থাকা বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের ওপর নির্ভরশীল ছিল না। জাতির প্রত্যেকের হৃদয়ে এখন একটা নতুন আইন আর চুক্তি লিখিত থাকবে। ঈশ্বর উৎসর্গের চেয়ে বরং ক্ষমা ও সহানুভূতি দাবি করেছেন। অ্যাক্সিয়াল যুগ ব্যক্তি বিশেষের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছিল। আমরা যেমন দেখেছি, অ্যাক্সিয়াল-যুগের সাধু ও পয়গম্বরগণ যেদিকেই তাকিয়েছেন কেবল নির্বাসন, ট্র্যাজিডি ও দুঃখ প্ৰত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু তাঁরা যে সত্যের সন্ধান করেছেন তা নিষ্ঠুরতা, অবিচার ও রাজনৈতিক পরাজয় সত্ত্বেও স্বস্তি খুঁজে পেতে সক্ষম করে তুলেছে। আমাদের কেবল নিপীড়নকারী রাষ্ট্রের হাতে মৃত্যুদণ্ড লাভের সময় সক্রেটিসের আলোকময় স্থৈর্য্য স্মরণ করলেই চলবে। তারপরও ব্যক্তি দুঃখ ভোগ করবে, মারা যাবে: প্রাচীন জাদুমন্ত্র দিয়ে নিয়তি খণ্ডনের কোনও প্রয়াস ছিল না; কিন্তু নারী বা পুরুষ জীবনের ট্র্যাজিডির মাঝেও এমন ত্রুটিপূর্ণ একটা জগতে অস্তি ত্বের অর্থ যোগানো এক ধরনের শান্তি বোধ করতে পারবে।
জাদুকরী নিয়ন্ত্রণের বদলে নবীন ধর্মগুলো বরং অস্তস্থ গভীরতার সন্ধান করেছে। সাধুগণ আর বাহ্যিক নীতির অনুসরণে সন্তুষ্ট ছিলেন না, বরং কর্মকাণ্ডের পূর্ববর্তী গভীর মনস্তাত্তিক অন্তর্মুখীতা সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠেছিলেন। অসচেতন শক্তি ও ক্ষীণ উপলব্ধ সত্যিকে আলোয় তুলে ধরাটা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সক্রেটিসের বেলায়, মানুষ ইতিমধ্যে সত্য জেনে গিয়েছিল, কিন্তু সেটা কেবল অন্তরের অস্পষ্ট স্মৃতি হিসাবে: তাদের এই জ্ঞান জাগিয়ে তোলার দরকার ছিল। প্রশ্ন তোলার দ্বান্দ্বিক উপায়ে পূর্ণ সজাগ হয়ে ওঠার প্রয়োজন ছিল। কনফুসিয়াস এতদিন পর্যন্ত নিশ্চিত ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার বাইরে রয়ে যাওয়া তাঁর জাতির প্রাচীন রীতিনীতি পর্যালোচনা করেছেন। আদি ঔজ্জ্বল্যে পুন:স্থাপন করার জন্যে তারা সম্মানের সঙ্গে যেসব মূল্যবোধকে তুলে রেখেছে সেগুলোকে অবশ্যই সচেতনভাবে লালন করতে হবে। কনফুসিয়াস ইতিপূর্বে কেবল অনুভূত ধারণাকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন এবং ভাসাভাসা, প্রায় অবোধ্য জ্ঞানকে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করতে চেয়েছেন। মানুষকে অবশ্যই নিজেকে পরীক্ষা করতে হবে, নিজের ব্যর্থতার কারণ বিশ্লেষণ করতে হবে এবং এভাবে জগতে সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলা আবিষ্কার করতে হবে যা মৃত্যুর কারণে অর্থহীন হয়ে যায়নি। অ্যাক্সিয়াল সাধুগণ প্রাচীন মিথোলিজ পরীক্ষা করেছেন, সেগুলোর পুনর্ব্যাখ্যা দিয়েছেন, প্রাচীন সত্যকে আবশ্যকীয়ভাবে নৈতিক মাত্ৰা দান করেছেন। নৈতিকতা ধর্মের কেন্দ্রীয় বিষয়ে পরিণত হয়। জাদুমন্ত্ৰ নয়, মানব জাতিকে নৈতিকতা দিয়ে নিজেকে জাগিয়ে তুলতে হবে এবং দায়িত্ব, নিজের পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জন করতে হবে; আমাদের চারপাশে চেপে আসা অন্ধকার থেকে মুক্তির খোঁজ করতে হবে। অতীত সম্পর্কে সজাগ ছিলেন সাধুগণ, বিশ্বাস করতেন যে মানুষ অস্তিত্বের মৌল বিষয়গুলো ভুলে যাবার কারণেই জগৎ কঠিন হয়ে উঠেছে। সবারই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, এমন এক পরম সত্তার–ঈশ্বর, নিব্বানা, তাও, ব্রহ্মা–অস্তিত্ব রয়েছে যা এই পৃথিবীর সমস্ত বিভ্রান্তির ঊর্ধ্বে এবং দৈনন্দিন জীবন যাপনের পরিস্থিতিতে তাঁকে সমন্বিত করার প্রয়াস পেয়েছেন।
সবশেষে, ব্রাহ্মণদের মতো গোপন সত্যিকে নিজেদের মাঝে আঁকড়ে রাখার বদলে অ্যাক্সিয়াল-সাধুগণ তা বাইরে প্রচার করতে চেয়েছেন।[২৬] ইসরায়েলের পয়গম্বরগণ সাধারণ মানুষের উদ্দেশে আবেগপ্রবণ হিতোপদেশ ও চমৎকার অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে বক্তব্য রাখতেন। যার সঙ্গে দেখা হতো তাকেই প্রশ্ন করতেন সক্রেটিস। সমাজ পরিবর্তনের প্রয়াসে ব্যাপকভাবে ঘুরে বেড়িয়েছেন কনফুসিয়াস। দরিদ্র, ক্ষুদ্র ও অভিজাতদের নির্দেশনা দিয়েছেন। এই সাধুরা তাঁদের তত্ত্বকে পরীক্ষা করতে ছিলেন বদ্ধপরিকর। ঐশীগ্রন্থ আর পুরোহিত সমাজের একচেটিয়া সম্পত্তি ছিল না বরং জনপদের কাছে নতুন ধর্মমত প্রচারের উপায়ে পরিণত হয়েছিল। গবেষণা ও বিতর্ক গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে পরিণত হয়েছিল। যারা সত্য সন্ধানে সংগ্রাম করেছে তাদের কাছে সত্যকে বাস্তবতা প্রমাণ করার প্রয়োজন ছিল। আমরা দেখব, গৌতম কত নিবিড়ভাবে অ্যাক্সিয়াল যুগের মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন এবং কীভাবে মানবীয় টানাপোড়েন সহ্য করার জন্যে আপন অনন্যতা নিয়ে এসেছিলেন।
অবশ্য তিনি যখন কাপিলাবাস্তুর পিতৃগৃহ ত্যাগ করেন, ভারতে তখন অ্যাক্সিয়াল পরিবর্তনের পালা চলছিল। ইতিহাসবিদ ও পণ্ডিতগণ উল্লেখ করেছেন যে, এই সমস্ত উদ্ভাবনমূলক আদর্শ রাজার এলাকায় সৃষ্টি হয়েছিল, বিসিই ষষ্ঠ শতকে যা নতুন ধরনের কেন্দ্রিকতা অর্জন করে।[২৭] রাজা ও মন্দিরের পুরোনো অংশীদারী হতে বণিকদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হচ্ছিল। এক নতুন ধরনের অর্থনীতি গড়ে তুলছিল তারা। তারা পুরোপুরি ব্যাখ্যা করতে না পারলেও, এইসব সামাজিক পরিবর্তন নিশ্চিতভাবে আধ্যাত্মিক বিপ্লবে অবদান রেখেছে। বাজার অর্থনীতি স্থিতাবস্থাকে দুর্বল করেছে: বণিকরা আর অনুগতের মতো পুরোহিত ও অভিজাতদের মানতে পারছিল না। তাদের নিজের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে, ব্যবসাক্ষেত্রে নিষ্ঠুর হবার জন্যে তৈরি থাকতে হয়েছে। এক নতুন নাগরিক শ্রেণী বিকাশ লাভ করছিল। নিজের হাতে ভাগ্যের নিয়ন্ত্রণ তুলে নেওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল তারা। এরা ছিল শক্তিমান, সম্মুখবর্তী ও উচ্চাভিলাষী। নতুন উদীয়মান আধ্যাত্মিক রীতিনীতির সাথে স্পষ্টতই সঙ্গতিপূর্ণ। অন্যান্য অ্যাক্সিয়াল অঞ্চলের মতো উত্তর ভারতের গঙ্গা নদীর আশপাশের সমতল ভূমি গৌতমের জীবৎকালে এই অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দী নাগাদ বহুদিন আগে আর্য আগ্রাসী বাহিনীর হাতে প্রতিষ্ঠিত আবশ্যিকভাবে গ্রাম্য সমাজ নতুন লৌহ-যুগের প্রযুক্তির কল্যাণে পরিবর্তিত হচ্ছিল, যা গভীর বন পরিষ্কার করে চাষাবাদের জন্যে নতুন জমিন বের করতে কৃষকদের সক্ষম করে তুলেছিল। বসতিকারীরা এই অঞ্চলে হাজির হওয়ায় তা ঘনবসতিপূর্ণ ও উচ্চ উৎপাদনশীল হয়ে ওঠে। পর্যটকগণ প্রচুর ফল, শস্য, তিল, জওায়ার, গম, সস্য আর বার্লির বর্ণনা দিয়েছেন, স্থানীয় জনগণের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ফলন হতো এসব ফলে তারা বিনিময় করতে পারত।[২৮] গাঙ্গেয় সমতল ইন্দো-সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হয়। গৌতমের জীবৎকালে মহাদেশের অন্যান্য এলাকা সম্পর্কে সামান্যই জানতে পারি আমরা। ছয়টি মহানগরী শিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হয়: সাবাস্তি, সাকেতা, কোসাম্বি, বারানসি, রাজাগহ ও চম্পা। নতুন বাণিজ্য পথের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল ওগুলো। নগরীগুলো ছিল উত্তেজনাকর জায়গা: সেগুলোর পথঘাট চমৎকাভাবে রঞ্জিত শকটে গিজগিজ করত, দূর-দূরান্ত থেকে পণ্য নিয়ে আসত সুবিশাল হাতির দল; ছিল জুয়া, থিয়েটার, নাচ, বেশ্যাবৃত্তি ও উচ্ছৃঙ্খল সরাইখানার জীবন। এসব আশপাশের গ্রামবাসীদের প্রবল আঘাত দিয়েছে। ভারতের সকল অংশের এবং সকল গোত্রের বণিকরা বাজারে জড়ো হতো; রাস্তাঘাটে নগর-কেন্দ্র, শহরতলীর বিলাসবহুল পার্কে নতুন দার্শনিক ধ্যানধারণা নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা চলত। শহরগুলো নতুন মানুষ–বণিক, ব্যবসায়ী ও মহাজনদের দখলে ছিল–যারা আর সহজে প্রাচীন গোত্র ব্যবস্থায় খাপ খাচ্ছিল না। তারা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের চ্যালেঞ্জ করতে যাচ্ছিল।[২৯] এসব ছিল অস্বস্তিকর, আবার উদ্দীপকও। শহরবাসীরা পরিবর্তনের ধার অনুভব করতে পারছিল।
অঞ্চলের রাজনৈতিক জীবনও বদলে গিয়েছিল। গাঙ্গেয় উপত্যকা মূলত ছোট ছোট কিছু রাজ্য ও অল্প কয়টি তথাকথিত প্রজাতন্ত্রের অধীনে শাসিত হতো, যেগুলো আদতে ছিল প্রাচীন ক্ল্যান ও গোত্রীয় ব্যবস্থাভিত্তিক গোষ্ঠী শাসন। প্রজাতন্ত্রগুলোর সবচেয়ে উত্তরের শাক্যয় জন্ম গ্রহণ করেন গৌতম। তাঁর বাবা শুদ্ধোদনা ছিলেন শাক্যের গোত্র ও তাদের পরিবার পরিচালনাকারী অভিজাত গোষ্ঠী সংঘের সদস্য। শাক্যবাসীরা নিদারুণ অহংকারী ও স্বনির্ভর ছিল। তাদের এলাকা বেশ দূরবর্তী ছিল বলে আর্য সংস্কৃতি কখনওই সেখানে শেকড় বিস্তার করতে পারেনি। তাদের গোত্র প্রথাও ছিল না। কিন্তু সময় বদলে যাচ্ছিল। শাক্যের রাজধানী কাপিলাবাস্তু ছিল নতুন বাণিজ্য পথগুলোর একটার গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য-কেন্দ্র। বাইরের জগৎ প্রজাতন্ত্রকে আক্রমণ শুরু করার ফলে ক্রমে মূলধারায় যোগ দিচ্ছিল।[৩০] মল্লা, কোলিয়া, বিদেহা, নয়া ও বাজ্জি প্রজাতন্ত্রগুলোর মতো শাক্য দুটি নতুন রাজ্য কোসালা ও মগধের কাছে আক্রান্ত বোধ করছিল। এদুটি রাজ্য গাঙ্গেয় সমতলের দুর্বলতর ও প্রাচীন-পন্থী রাজ্যগুলোকে আগ্রাসী ও নির্মমভাবে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসছিল।
কোসালা ও মগধ পুরোনো প্রজাতন্ত্রেগুলোর চেয়ে ঢের দক্ষতার সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছিল। পুরোনো রাজ্যগুলোয় লাগাতার অন্তর্দ্বন্দ্ব্ব ও গৃহবিবাদ লেগেই ছিল। আধুনিক এই রাজ্যগুলো আমলাতন্ত্র ও সেনাবাহিনীকে সুশৃঙ্খলিত করেছিল যারা সামগ্রিকভাবে গোত্রের কাছে নয়, কেবল রাজার প্রতিই আনুগত্য স্বীকার করত। এর মানে ছিল, প্রত্যেক রাজার নিজস্ব যুদ্ধ- মেশিন ছিল যেটা তাঁকে তাঁর রাজত্বে শৃঙ্খলা আরোপ ও আশপাশের এলাকা অধিকারের শক্তি যুগিয়েছে। আধুনিক এই রাজ্যগুলো নতুন বাণিজ্য পথগুলোও দক্ষতার সঙ্গে পাহারা দিতে সক্ষম ছিল। রাজ্যের অর্থনীতি যাদের ওপর নির্ভরশীল ছিল সেই বণিকদের খুশি করেছিল এটা।[৩১] অঞ্চলটি নতুন ধরনের স্থিতিশীলতা ভোগ করলেও সেজন্যে কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। নতুন সমাজের সহিংসতা ও নিষ্ঠুরতায় অনেকেই অস্বস্তিতে ভুগছিল, যেখানে রাজারা জনগণের উপর তাঁদের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে পারতেন, অর্থনীতি পরিচালিত হতো প্রলোভনে; মহাজন ও বণিকরা পরস্পরের সঙ্গে আগ্রাসী প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকায় পরস্পরকে শিকারে পরিণত করত। প্রচলিত মূল্যবোধ যেন গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল, হারিয়ে যাচ্ছিল পরিচিত জীবন ধারা। সেই জায়গা দখল করে নেওয়া ব্যবস্থা ছিল ভীতিকর, অচেনা। জীবনকে অসংখ্য মানুষের কাছে বোঝা মনে হওয়াটা বিস্ময়কর ছিল না, সাধারণত ‘ভোগান্তি’ হিসাবে যার অনুবাদ করা হয়, তবে ‘অসন্তোষজনক’, ‘ত্রুটিপূর্ণ’ ও ‘কুটিল’ জাতীয় শব্দেই যার অর্থ বেশি বোঝানো যায়।
এমনি পরিবর্তনশীল সমাজে প্রাচীন আর্য-ধর্ম ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্ম ক্রমবর্ধমান হারে বেমানান হয়ে উঠছিল। প্রাচীন আচার প্রতিষ্ঠিত গ্রাম্য সমাজের উপযোগি ছিল, কিন্তু শহর-নগরের অধিকতর গতিশীল জগতে দুর্বহ ও সেকেলে মনে হতে শুরু করেছিল। অবিরাম চলার ওপর থাকায় বণিকেরা আগুন জ্বালিয়ে রাখতে পারত না, উপসোথা দিবসও পালন করতে পারত না। নতুন এই মানুষগুলো গোত্র প্রথায় ক্রমশঃ বেমানান হয়ে যাচ্ছিল বলে অনেকেরই তাদের একটা আধ্যাত্মিক শূন্যতার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়েছে। পশুপালন অর্থনীতির চালিকা শক্তি থাকার সময় পশু-বলী তাৎপর্যবহ ছিল, কিন্তু নতুন রাজ্যগুলো কৃষিজাত পণ্যের উপর নির্ভরশীল ছিল। পশু হয়ে উঠছিল দুষ্প্রাপ্য, ফলে বলী অপচয় ও নিষ্ঠুর ঠেকেছে-বর্তমানে জনজীবনকে বৈশিষ্ট্যায়িত করে তোলা সহিংসতার চড়া স্মারক। নাগরিক সমাজগুলো যখন নিজেদের উপর নির্ভরশীল স্বনির্মিত মানুষের প্রভাবে ছিল সেই সময় মানুষ ক্রমবর্ধমানহারে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যের ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে ও আধ্যাত্মিক নিয়তি নিজের নিয়ন্ত্রণে আনতে চেয়েছে। তাছাড়া, পশু বলী কাজে আসেনি। ব্রাহ্মণরা যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে এইসব আচার অনুষ্ঠান (কম্ম ) মানুষের জন্যে ঐশ্বর্য ও বৈষয়িক সাফল্য এনে দেবে। কিন্তু প্রতিশ্রুত এইসব সুবিধা সাধারণত বাস্তবায়িত হতে পারেনি। নতুন অর্থনৈতিক পরিবেশে নগরবাসীরা সুবিধাজনক বিনিয়োগ বয়ে আনার মতো কাজে মনোনিবেশ করতে চেয়েছে।
বাজার অর্থনীতি প্রভাবিত আধুনিক রাজ্য ও শহরগুলো গাঙ্গেয় অঞ্চলের জাতিগুলোকে পরিবর্তনের হার সম্পর্কে দারুণ সজাগ করে তুলেছিল। নগরবাসীরা সমাজের দ্রুত বদলে যাওয়ার ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল: এর অগ্রগতি পরিমাপ করতে পেরেছে তারা; বছরের পর বছর সবাই একই কাজ করে এমনি গ্রাম্য সমাজের পুনরাবৃত্তিমূলক ছন্দের চেয়ে একেবারে ভিন্ন একটা জীবন ধারার স্বাদ আস্বাদন করতে পারছিল তারা, যে সমাজ পরিবর্তনের ওপর নির্ভরশীল ছিল। শহরের মানুষ উপলব্ধি করতে শুরু করেছিল যে, তাদের কর্মকাণ্ডের (কম্ম) দীর্ঘমেয়াদী পরিণাম রয়েছে যা তারা নিজেরা হয়তো দেখতে পাবে না কিন্তু ঠিকই বুঝতে পেরেছিল যে আগামী বংশধরদের তা প্রভাবিত করবে। অতি সাম্প্রতিক কালে উদ্ভুত পুনর্জন্মের মতবাদ দারুণ প্রাচীন বৈদিক ধর্মের চেয়ে চলমান বিশ্বে অধিকতর জুৎসই ছিল। কম্মের তত্ত্ব বলে যে, নিয়তির জন্যে দায়ী করার মতো কেউ নেই, আমাদের কর্মকাণ্ডই সুদূরবর্তী ভবিষ্যতে অনুরণন তুলবে। একথা ঠিক যে কম্ম মানুষকে ক্লান্তিকর সামসারার চক্র থেকে মুক্তি দেবে না, তবে সৎকম্ম মূল্যবান প্রতিদান বয়ে আনবে কেননা তা পরের জীবনে আরও বেশি উপভোগ্য অস্তিত্ব নিশ্চিত করবে। কয়েক প্রজন্ম আগেও পুনর্জন্মের মতবাদ দারুণ বিতর্কিত ছিল, অল্প কিছু লোকের জানা ছিল তা। কিন্তু গৌতমের সময়ে মানুষ যখন একেবারে নতুনভাবে কাজ ও কারণের ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠেছিল, তখন সবাই তা বিশ্বাস করেছে-এমনকি খোদ ব্রাহ্মণরাও।[৩২]
কিন্তু অন্যান্য অ্যাক্সিয়াল দেশের মতো উত্তর ভারতের জনগণ অন্যান্য ধর্মীয় ধ্যানধারণা ও আচার-আচরণ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেছিল যেগুলো তাদের পরিবর্তিত অবস্থায় বেশ প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্ক স্থাপন করেছে। গৌতমের জন্মের অল্প আগে গাঙ্গেয় সমতলের পশ্চিম এলাকার একদল সন্ন্যাসী প্রাচীন বৈদিক ধর্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে গোপন বিপ্লব সংগঠিত করেছিলেন। তাঁরা এক ধারাবাহিক টেক্সট সৃষ্টি শুরু করেছিলেন যেগুলো গুরু থেকে শিষ্যের কাছে গোপনে হস্তাস্তরিত হতো। নতুন এই ধর্মগ্রন্থগুলোর নাম ছিল উপনিষদ, এ নামটি বিপ্লবাত্মক লোক-জ্ঞানের নিগূঢ় প্রকৃতির ওপর জোর দিয়েছে; কেননা তা সংস্কৃত উপ-নি-সাদ (নিকটে উপবেশন) হতে নেওয়া। উপনিষদগুলো বাহ্যত প্রাচীন বেদের উপর ভিত্তি করে রচিত হলেও সেগুলোকে পুনর্ব্যাখ্যা করে অধিকতর আধ্যাত্মিক ও অন্তর্গত তাৎপর্য দিয়েছে। এখানেই অ্যাক্সিয়াল যুগের অন্যতম প্রধান ধর্মমত বর্তমানে হিন্দুধর্ম নামে পরিচিত ধর্মের সূচনা স্থির হয়েছিল। সন্ন্যাসীদের আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের লক্ষ্য ছিল মহাবিশ্বের নৈর্ব্যক্তিক মূল সুর এবং অস্তিত্বমান সমস্ত কিছুর উৎস ব্রহ্মার পরম সত্তা। কিন্তু ব্রহ্মা স্রেফ একজন দূরবর্তী ও দুর্ভেয় সত্তা নন; সর্বব্যাপী সত্তাও যা জীবিত সমস্ত কিছুকে আবৃত করে আছে। আসলে উপনিষদীয় অনুশীলনের কল্যাণে একজন শিক্ষাব্রতী আপন সত্তার গভীরে ব্রহ্মার উপস্থিতি দেখতে পাবে। ব্রাহ্মণদের শিক্ষানুযায়ী পশুবলীতে মুক্তি নিহিত নয়, বরং এই উপলব্ধিতে যে দেবতাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ পরম, চিরন্তম সত্তা ব্রহ্মা মানুষের গভীরতম সত্তার (আত্মা) অনুরূপ।[৩৩]
আমরা যেমন দেখব, চিরন্তন ও পরম সত্তার ধারণা, গৌতমকে দারুণ পীড়া দেবে। এক অসাধারণ আত্ম-দর্শন ছিল এটা। কারও গভীরতম সত্তা ব্রহ্মার অনুরূপ, এই ধারণায় বিশ্বাস স্থাপন সাধুদের পবিত্র সম্ভাবনায় চমকপ্রদ বিশ্বাসের আচরণ ছিল। এই দর্শনের ধ্রুপদী প্রকাশ দেখা যায় প্রাথমিক চান্দোগ্যা উপনিষদে। ব্রাহ্মণ উদ্দালোকা তাঁর বৈদিক জ্ঞানে গর্বিত ছেলে শ্রেতাকেতুকে প্রাচীন ধর্মের সীমাবদ্ধতা দেখাতে চেয়েছিলেন, শ্রেতাকেতুকে একপাত্র পানিতে এক টুকরো লবণ মেশাতে বলেন তিনি। পরদিন সকালে দৃশ্যত লবণ অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু শ্রেতাকেতু যখন পানিতে চুমুক দিলো, দেখা গেল, লবণ দেখা না গেলেও সমস্ত পানিতে মিশে গেছে। ঠিক ব্রহ্মার মতো, ব্যাখ্যা করলেন উদ্দালোকা: তুমি দেখতে না পেলেও আছে। ‘সমগ্র বিশ্বের আপন সত্তা(আত্মা) হিসাবে এই প্রাণ সত্তা (ব্রহ্মা) রয়েছে। এটাই সত্তা, সেটাই তুমি শ্রেতাকেতু![৩৪] এটা আসলেই বিদ্রোহমূলক; আপনি যখন বুঝতে পারবেন যে, আপনিসহ সমস্ত কিছুতে পরম সত্তা আছেন, তখন আর অভিজাত পুরোহিত সমাজের প্রয়োজন থাকবে না। নিষ্ঠুর অর্থহীন পশুবলী ছাড়াই মানুষ আপন সত্তায় নিজেই পরমকে খুঁজে পাবে।
তবে ব্রাহ্মণদের প্রাচীন ধর্ম বিশ্বাস প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে উপনিষদের সাধুরা একাকী ছিলেন না। গাঙ্গেয় অঞ্চলের পূর্বাংশের বনচারী সন্ন্যাসী ও ভাববাদীরা উপনিষদের আধ্যাত্মিকতার সাথে পরিচিত ছিলেন না। তখনও তা পশ্চিম সমতলে গোপন নিগূঢ় ধর্মবিশ্বাস হিসাবে কেন্দ্রীভূত ছিল। অবশ্য নতুন ধারণার কিছু কিছু লোক পরম্পরায় প্রকাশিত হয়ে পড়েছিল। পূর্ব-গাঙ্গেয় এলাকায় ব্রহ্মার কোনও আলোচনা ছিল না, বুদ্ধ ধর্মগ্রন্থে যাঁর কোনও উল্লেখ করা হয়নি, কিন্তু পরম নীতির একটি লোক ভাষ্য নতুন দেবতা ব্রহ্মার বিশ্বাসে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। বলা হয়েছে, যিনি সর্বোচ্চ স্বর্গে বাস করেন। গৌতম ব্রাক্ষণের কথা শুনেছেন বলে মনে হয় না, তবে ব্রহ্মা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন তিনি, যিনি, আমরা দেখব, গৌতমের ব্যক্তি-নাটকে ভূমিকা রেখেছেন।[৩৫] গৌতম কাপিলাবাস্তু ত্যাগ করে পূর্বাঞ্চলের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন। জীবনের বাকি সময় কোসালা, মগধ ও লাগোয়া প্রাচীন রাজ্যগুলোয় ভ্রমণ করে কাটিয়েছেন। এখানে প্রাচীন আর্য প্রথার আধ্যাত্মিক প্রত্যাখ্যান অধিকতর বাস্ত বধর্মী বাঁক নিয়েছিল। মানুষ পরম সত্তার প্রকৃতি নিয়ে অধিবিদ্যিক আঁচ- অনুমানের উৎসাহী ছিল না। ব্যক্তিগত মুক্তি নিয়ে অধিকতর চিন্তিত ছিল তারা। বনচারী-সাধুরা দুর্ভেয় ব্রহ্মা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু তাঁরা অন্তস্থ পরম সত্তা, আত্মাকে জানতে চেয়েছেন। এই চিরন্তন, সর্বব্যাপী নীতির নাগাল পাওয়ার নানান উপায় বের করছিলেন তাঁরা। সত্তার মতবাদ আকর্ষণীয় ছিল, কারণ জীবনের দুঃখ-কষ্ট হতে মুক্তি লাভ আয়ত্তের মধ্যেই রয়েছে বলেই বোঝানো হয়েছে এখানে, এজন্যে কোনও পুরোহিতের মধ্যস্থতার প্রয়োজন নেই। এটা নতুন সমাজের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং আত্ম-নির্ভরতার বিশ্বাসের সঙ্গে মানানসই ছিল। সন্ন্যাসী একবার আপন সত্তার সন্ধান লাভ করার পর এক গভীর স্তরে উপলব্ধি করবেন যে দুঃখ-কষ্ট ও মৃত্যুই মানবীয় অবস্থার শেষ কথা নয়। কিন্তু কেমন করে সন্ন্যাসী এই সত্তার দেখা পাবেন এবং সামসারার অর্থহীন চক্র হতে মুক্তি পাবেন? যদিও সত্তার অস্তিত্ব প্রতিটি মানুষের মাঝেই থাকার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সন্ন্যাসীরা তাঁর দেখা পাওয়া কঠিন বলে আবিষ্কার করেছেন।
পূর্ব-গাঙ্গেয় এলাকার আধ্যাত্মিকতা অনেক বেশি লোকানুবর্তী ছিল। পশ্চিমে উপনিষদীয় সাধুগণ তাঁদের মতবাদ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আড়াল করে রেখেছিলেন: পুবে সাধারণ মানুষ আন্তরিকভাবে এইসব প্রশ্ন নিয়ে বিতর্ক করেছে।[৩৬] আমরা যেমন দেখেছি, তারা ভিক্ষু সন্ন্যাসীদের অর্থহীন পরজীবী হিসাবে নয় বরং বীরসুলভ অগ্রগামী হিসাবে দেখেছে। বিদ্রোহী হিসাবেও সম্মান দেখানো হয়েছে তাঁদের। উপনিষদীয় সাধুদের মতো সন্ন্যাসীরা প্রাচীন বৈদিক ধর্মকে ঔদ্ধত্যের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অনুসন্ধানের সূচনায় একজন নবীশ পাব্বজ্জ (যার অর্থ ‘সামনে গমন’) নামে পরিচিত অনুষ্ঠানে যোগ দেয়: এমন একজন মানুষে পরিণত হয় সে আক্ষরিক অর্থেই যে আর্য সমাজ হতে বের হয়ে গেছে। আচারের দাবি অনুযায়ী ত্যাগী গোত্রের সকল বাহ্যিক চিহ্ন খুলে ফেলে ও ব্যবহৃত তৈজসপত্র অগ্নিতে উৎসর্গ করে। এরপর থেকে তাকে বলা হবে সন্ন্যাসী (ধর্ম-ত্যাগী) এবং তার গেরুয়া পোশাক তার বিদ্রোহের প্রতাঁকে পরিণত হবে। তার গেরুয়া পোশাক বিদ্রোহের প্রতাঁকে পরিণত হবে। সবশেষে নব্য সন্ন্যাসী সম্ভবত অধিকতর অস্তস্থ ধর্ম বেছে নেওয়ার ঘোষণার উপায় হিসাবে আচরিক ও প্রতীকী ঢঙে পবিত্র অগ্নি গিলবে।[৩৭] ব্যবস্থার মেরুদণ্ড সংসারী মানুষের জীবন প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে পুরোনো পৃথিবীতে স্ব-অবস্থান স্বেচ্ছায় প্রত্যাখ্যান করেছে সে: বিবাহিত পুরুষ অর্থনীতি চালু রাখে, পরবর্তী প্রজন্মের জন্ম দেয়, সকল গুরুত্বপূর্ণ উৎসর্গের ব্যয় মেটায় এবং সমাজের রাজনৈতিক জীবনের তত্ত্বাবধান করে। কিন্তু সন্ন্যাসীরা এইসব দায়িত্ব সরিয়ে রেখে এক ধরনের রেডিক্যাল মুক্তির সন্ধান করেন। তাঁরা গৃহের কাঠামোর স্থান ছেড়ে বুনো বনজঙ্গল বেছে নিয়েছেন: তাঁরা আর গোত্রের বিধিনিষেধের পাত্র নন, কোনওভাবেই জন্মগত দুর্ঘটনার কারণে কোনও কর্মকাণ্ড হতে বঞ্চিত নন। বণিকদের মতোই চলিষ্ণু ছিলেন তাঁরা, ইচ্ছামতো জগৎ ঘুরে বেড়াতে পারতেন। নিজের কাছে ছাড়া কারও কাছে জবাবদিহি করতে হতো না। সুতরাং, তাঁরাও বণিকদের মতো যুগের নতুন মানুষ ছিলেন, যাঁদের সমগ্র জীবনধারা সেই সময়কে বৈশিষ্ট্যায়িত করা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের বর্ধিত বোধ প্রকাশ করেছে।
সুতরাং, গৃহত্যাগ করতে গিয়ে গৌতম অধিকতর প্রথাগত বা এমনকি প্রাচীন জীবন ধারার পক্ষে আধুনিক বিশ্ব ত্যাগ করছিলেন না (যেমনটা বর্তমানের সন্ন্যাসীরা করছেন বলে প্রায়শঃই ধারণা করা হয়), বরং পরিবর্তনের অগ্রসারিতে ছিলেন তিনি। অবশ্য তাঁর পরিবার এই দৃষ্টিভঙ্গির অংশীদার হবে এমনটা আশা করা যায় না। শাক্য রাজ্য এমন বিচ্ছিন্ন ছিল বলে নিম্নস্থ গাঙ্গেয় সমতলে বিকাশমান সমাজ হতে একেবারে আলাদা ছিল। আমরা যেমন দেখেছি, এমনকি বৈদিক সংস্কৃতিও আত্মীকরণ করতে পারেনি। শাক্যের অধিকাংশ মানুষের কাছে নতুন ধ্যান-ধারণা অচেনা মনে হয়ে থাকবে। তা সত্ত্বেও বনচারী সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহের সংবাদ নিঃসন্দেহে রাজ্যে পৌঁছেছিল; আলোড়িত করেছে তরুণ গৌতমকে। আমরা যেমন দেখেছি, পালি টেক্সট তাঁর গৃহত্যাগের সিদ্ধান্তের অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়, তবে গৌতমের গৃহত্যাগের আরেকটি বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে যেটা কিনা পাব্বজ্জ্যের গভীরতম তাৎপর্য তুলে ধরে।[৩৮] নিদান কথার মতো কেবল পরবর্তী সময়ের পরিবর্ধিত জীবনীগুলোতেই এটা মেলে, যা সম্ভবত সিই পঞ্চম শতাব্দীতে লেখা হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও আমরা এই কাহিনীটি পরবর্তী সময়ের বুদ্ধ রচনাবলীতে পেলেও পালি কিংবদন্তীসমূহের মতোই সমান প্রাচীন হতে পারে। কোনও কোনও পণ্ডিত বিশ্বাস করেন যে, পরবর্তী কালের এই ধারাবাহিক জীবনীগুলো গৌতমের মৃত্যুর মোটামুটি একশো বছর পরে পালি বিধান চূড়ান্ত রূপ নেওয়ার সময় রচিত প্রাচীন বর্ণনার ভিত্তিতেই রচিত হয়েছিল। পালি কিংবদন্তীসমূহ নিশ্চিতভাবে এই কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত ছিল, কিন্তু সেগুলো একে গৌতম নয়, বরং তাঁর পূর্বসুরি, বুদ্ধ বিপাসির বলে বর্ণনা করেছে, যিনি পূর্ববর্তী কালে আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।[৩৯] সুতরাং কাহিনীটি আদর্শ ধরনের, সকল বুদ্ধের বেলায়ই প্রযোজ্য। এটা গৌতমের গৃহত্যাগের পালি ভাষ্যকে চ্যালেঞ্জ করেনি, আমাদের হিসাবে ঐতিহাসিকভাবে সঠিকও বোঝানো হয়নি। পরিবর্তে প্রবলভাবে পৌরাণিক এই কাহিনীটি স্বর্গীয় হস্তক্ষেপ ও জাদুময় ঘটনাবলীসহ পাবজ্জ্যের জটিল ঘটনার একটি বিকল্প ব্যাখ্যা তুলে ধরে। এটাই সকল বুদ্ধকে–গৌতম বিপাস্সির চেয়ে কম নন–তাঁদের অনুসন্ধানের সূচনায় করতে হবে; প্রকৃতপক্ষে আধ্যাত্মিক জীবনে পদার্পন করার সময় আলোক সন্ধানী প্রত্যেককে পরিবর্তনের এই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যেতে হবে। কাহিনীটি প্রায় অ্যাক্সিয়াল যুগ আধ্যাত্মিকতার নজীর। একজন মানুষ কেমন করে অ্যাক্সিয়াল-যুগের চাহিদা অনুযায়ী তার দর্শন সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন হয়ে ওঠে তাই দেখায়। মানুষ যখন দুঃখ-কষ্টের অনিবার্য বাস্তবতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে তখনই শুধু পুরোপুরি মানুষ হয়ে উঠতে শুরু করতে পারে। নিদান কথার কাহিনী প্রতীকী। এর সর্বজনীন প্রভাব রয়েছে, কারণ অজাগ্রত নারী-পুরুষ জীবনের দুঃখ-কষ্টকে উপেক্ষা করতে চায়; ভান করে যেন এর সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই। এমন উপেক্ষা কেবল নিষ্ফলই নয় (কারণ কেউই জ্বালা-যন্ত্রণা হতে মুক্ত নয় এবং জীবনের এইসব সত্য সবসময়ই হামলা চালাবে), বরং বিপজ্জনকও। কেননা, মানুষকে তা এমন এক কুহকে বন্দি করে যা তার আধ্যাত্মিক বিকাশ ব্যাহত করে।
এভাবে নিদান কথা আমাদের বলছে, সিদ্ধার্থের যখন বয়স মাত্র পাঁচ দিন, তাঁর বাবা শুদ্ধোদোন একশোজন ব্রাহ্মণকে ভোজে আমন্ত্রণ জানান, যেন তাঁরা শিশুর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলবার জন্যে চিহ্নের খোঁজে দেহ পরীক্ষা করতে পারেন। আটজন ব্রাহ্মণ উপসংহারে পৌঁছলেন যে, শিশুটির সামনে রয়েছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, তিনি হয় একজন বুদ্ধে পরিণত হবেন, যিনি পরম আধ্যাত্মিক আলোকপ্রাপ্ত হয়েছেন, কিংবা হবেন সর্বজনীন রাজা, জনপ্রিয় কিংবদন্তীর নায়ক, যিনি, বলা হয়ে থাকে, জগৎ শাসন করবেন। তাঁর একটি বিশেষ স্বর্গীয় রথ থাকবে। তার চারটে চাকার প্রতিটি পৃথিবীর চারদিকে ঘুরবে। এই জগৎ- সম্রাট বিশাল সেনাদল নিয়ে স্বর্গে ঘূরে বেড়াবেন এবং ‘ন্যায়বিচারের চাকা ঘোরাবেন’, সমগ্র জগতে ন্যায় বিচার ও সঠিক ধারা প্রতিষ্ঠা করবেন। কোসালা ও মগধের নতুন রাজতন্ত্রের পরিষ্কার প্রভাব ছিল এই মিথে। গৌতমের সমগ্র জীবনে তাঁকে নিয়তির এই বিকল্পের মোকাবিলা করতে হয়েছে। বিশ্ব-সম্রাটের (চক্কবত্তী) ইমেজ প্রতীকী বিকল্প-অহমে পরিণত হবে, শেষ পর্যন্ত তাঁর অর্জিত সমস্ত কিছুর বিপরীত চক্কবতী শক্তিমান হতে পারেন, তাঁর রাজত্ব জগতের জন্যে উপকারীও হতে পারে; কিন্তু আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে তিনি আলোকিত মানুষ নন, কেননা তার জীবন সম্পূর্ণভাবে শক্তির উপর নির্ভরশীল। কোন্দান্না নামে এক ব্রাহ্মণের বিশ্বাস ছিল, শিশু সিন্ধার্থ কখনওই চক্কবত্তী হবেন না, বরং তিনি গৃহস্থ মানুষের আরামদায়ক জীবন ত্যাগ করে অজ্ঞতা ও জগতের বিপর্যয় হতে উত্তীর্ণ হয়ে বুদ্ধে পরিণত হবেন।[৪০]
এই ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে খুশি ছিলেন না শুদ্ধোদোন। ছেলে যেন চক্কবত্তী না হয় সে ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন তিনি, যা তাঁর কাছে জগৎ অস্বীকারকারী সাধুর জীবনের চেয়ে ঢের বেশি কাঙ্ক্ষিত মনে হয়েছে। কোন্দান্না তাঁকে বলেছিলেন, সিদ্ধার্থ একদিন চারটি জিনিস দেখতে পাবেন–একজন জরাগ্রস্থ মানুষ, একজন রোগী, একটা মরদেহ এবং একজন সাধু–যা তাঁকে গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়ে ‘বেরিয়ে যেতে’ অনুপ্রাণিত করবে। শুদ্ধোদোন তাই ছেলেকে এইসব অস্বস্তিকর দৃশ্য হতে আড়াল করার সিদ্ধান্ত নেন: বিপর্যয়কর দৃশ্য দূরে ঠেলে রাখার জন্যে প্রসাদের চারপাশে প্রহরা বসানো হয়েছিল। কার্যত বন্দিতে পরিণত হয়েছেন গৌতম। যদিও বিলাসীতার আপাত সুখী জীবন কাটাচ্ছিলেন তিনি। গৌতমের প্রমোদ প্রাসাদ অস্বীকৃতি প্রকাশকারী মনের একটা জোরাল ইমেজ। আমরা যতক্ষণ আমাদের চারপাশে থেকে ঘিরে রাখা সর্বজনীন যন্ত্রণার থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখতে চাই, ততক্ষণ আমরা পরিণত ও আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টির অযোগ্য আমাদের এক অনুন্নত ভাষ্যে বন্দি হয়ে থাকি। তরুণ সিদ্ধার্থ এক ধরনের বিভ্রান্তিতে বাস করছিলেন, কেননা জগৎ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে প্রকৃত অবস্থার মিল ছিল না। পরবর্তী সময়ের বুদ্ধ ট্র্যাডিশন যাকে নিন্দা করবে শুদ্ধোদোন ঠিক সেই রকম একজন কর্তৃত্ব-পুরুষ। নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছেলের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন তিনি, তাঁকে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে দিতে অস্বীকার গেছেন। এই জাতীয় নিপীড়ন কেবল আলোকনকেই ব্যাহত করতে পারে, কেননা এটা মানুষকে এমন এক সত্তায় আবদ্ধ করে যা সঠিক নয়; শিশুসুলভ অজাগ্রত অবস্থা।
কিন্তু দেবতাগণ হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁরা জানতেন গৌতমের বাবা মেনে নিতে অস্বীকার করলেও তিনি একজন বোধিসত্তা; বুদ্ধ হওয়াই যাঁর নিয়তি। অবশ্য দেবতারা গৌতমকে আলোকনের দিকে পরিচালিত করেননি, কারণ তাঁরাও সামসারায় বন্দি এবং মানুষের মতোই মুক্তি লাভের পথ শেখানোর জন্যে একজন বুদ্ধের প্রয়োজন ছিল তাঁদের। কিন্তু দেবতাগণ বোধিসত্তাকে অতি-প্রয়োজনীয় ধাক্কা দিতে পারতেন। তাঁর বয়স ঊনত্রিশ বছর হলে, তাঁরা সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে, যথেষ্ট দীর্ঘ সময় বোকার স্বর্গে বাস করেছেন গৌতম, তো তাঁরা তাঁদেরই একজনকে জরাগ্রস্ত মানুষের বেশে প্রমোদ-বাগিচায় পাঠালেন, শুদ্ধোদোনের প্রহরীদের ফাঁকি দেওয়ার জন্যে অলৌকিক ক্ষমতা কাজে লাগাতে পেরেছিলেন তিনি। বাগিচায় শকট চালানোর সময় এই বুদ্ধকে দেখে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন গৌতম। রথচালক চান্নাকে লোকটার কী হয়েছে জিজ্ঞেস করলেন। চান্না ব্যাখ্যা করল, স্রেফ বুড়িয়ে গেছে সে: যারা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকে তাদের সবাইকে এমনি ক্ষয়ে যেতে হবে। গভীর দুঃখ নিয়ে প্রাসাদে ফিরে গেলেন গৌতম।
ঘটনা জানতে পেরে পাহারা দ্বিগুণ করে দিলেন শুদ্ধোদোন। ছেলেকে ভিন্নমুখী করতে বিনোদনের মাত্রা বাড়িয়ে দিলেন–কিন্তু কোনও লাভ হলো না। আরও দুটো উপলক্ষ্যে দেবতারা অসুস্থ ও শবদেহের রূপ ধরে গৌতমের সামনে হাজির হলেন। সবশেষে গৌতম ও চান্না সন্ন্যাসীর গেরুয়া পোশাক পরা এক দেবতার পাশ দিয়ে রথ চালিয়ে গেলেন। দেবতাদের অনুপ্রেরণায় চান্না গৌতমকে জানাল, এই মানুষটি জগৎ সংসার ত্যাগ করেছেন। তারপর এমন আবেগের সঙ্গে সন্ন্যাস জীবনের গুণ গাইল ফলে খুবই চিন্তিত মনে ঘরে ফিরে এলেন গৌতম। সে রাতে জেগে উঠে দেখলেন ওইদিন সন্ধ্যায় যারা তাঁর মনোরঞ্জনে ব্যস্ত ছিল সেই কবি আর নাচিয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে। তাঁর শয্যার চারধারে সুন্দরী মেয়েরা আলুথালু হয়ে শুয়ে আছে: ‘কারও শরীর লালা- থুতুতে পিচ্ছিল, অন্যরা দাঁত কাটছে, ঘুমের ঘোরে অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছে; কেউ কেউ আবার হাঁ করে ঘুমোচ্ছে।’ জগৎ সম্পর্কে গৌতমের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রতিটি সত্তার সামনে অপেক্ষমান ভোগান্তির ব্যাপারে সচেতন হয়ে ওঠায় সবকিছু কুৎসিৎ মনে হলো তাঁর-অনাকর্ষণীয় বটে। জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণাকে আড়াল করে রাখা পর্দা ছিঁড়ে পড়েছিল, জগৎ-সংসারকে মনে হয়েছে কষ্টের কারাগার, অর্থহীন। “কী অসহনীয়, শ্বাসরুদ্ধকর!’ চেঁচিয়ে উঠলেন গৌতম। লাফিয়ে বিছানা থেকে নামলেন তিনি, সেই রাতেই ‘অগ্রসর’ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।[৪১]
মানবীয় অবস্থার অনিবার্য অংশ দুঃখ-কষ্টকে দূরে রাখার চেষ্টা সবসময়ই প্রলুব্ধকারী, কিন্তু একবার আমাদের সৃষ্টি করা সতর্কতার প্রাচীর ভেঙে পড়লে আমরা আর জগতকে আগের মতো করে দেখতে পারি না। জীবন অর্থহীন মনে হয় এবং একজন অ্যাক্সিয়াল-যুগ অগ্রযাত্রী পুরোনো প্রচলিত ধরণ ভেঙে বের হয়ে আসতে নিজেকে বাধ্য মনে করবেন, এই যন্ত্রণার সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার নতুন পথ বের করার চেষ্টা করবেন। কেবল মনের অন্তস্থ আশ্রয়ের সন্ধান পাবার পরই জীবন আবারও অর্থপূর্ণ ও মূল্যবান মনে হবে। গৌতম দুঃখকে তাঁর অন্তরে অনুপ্রবেশ করার সুযোগ দেওয়ার পরেই তাঁর জগৎ ভেঙে পড়েছে। আমাদের অনেকেই দুঃখ-কষ্টকে দূরে ঠেলে রাখার জন্যে চারপাশে যে দেয়াল তুলে রাখি তিনি সেই কঠিন আস্তরণকে ভেঙে ফেলেছেন। কিন্তু দুঃখ-কষ্টকে প্রবেশ করতে দেওয়ার পরেই তাঁর অনুসন্ধান শুরু হতে পেরেছে। বাড়ি ছাড়ার আগে স্ত্রী-সন্তানকে শেষ বারের মতো দেখবেন বলে পা টিপে টিপে ওপরে গিছেন তিনি, কিন্তু বিদায়ের কথা বলতে পারেননি। সবার অজান্তে প্রাসাদ ছেড়ে বের হয়ে গেছেন। কানসাকা নামের ঘোড়ায় চেপে শহরের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেছেন তিনি। তাঁর বিদায় রোধ করার জন্যে মরিয়া হয়ে লাগাম ধরে রাখে চান্না। তাঁকে বেরিয়ে যাবার সুযোগ দিতে নগর তোরণ খুলে দিলেন দেবতারা। কাপিলাবাস্তু ছাড়ার পর মাথা মুড়িয়ে গেরুয়া পোশাক পরলেন গৌতম। তারপর চান্না ও কানসাকাকে বাবার বাড়িতে ফেরত পাঠালেন। আরেকটি বুদ্ধ-কিংবদন্তীতে আমাদের বলা হচ্ছে, ঘোড়াটা দুঃখে মারা যায়, কিন্তু বুদ্ধের আলোকপ্রাপ্তিতে তার অবদানের পুরস্কার হিসাবে মহাবিশ্বের কোনও এক স্বর্গে দেবতা হিসাবে পুনর্জন্ম পেয়েছিল সে।
পূর্ণাঙ্গ অনুসন্ধান শুরু করার আগে গৌতমকে শেষবারের মতো আরেকটি প্রলোভনের মোকাবিলা করতে হয়েছে। এই জগতের প্রভু, পাপ, লোভ ও মৃত্যুর দেবতা মারা সহসা ভীতিকরভাবে তাঁর সামনে হাজির হলেন। ‘সন্ন্যাসী হয়ো না! জগৎ অস্বীকার করো না।’ মিনতি জানালেন মারা। আর মাত্র এক সপ্তাহ ঘরে থাকলেই চক্কবত্তী হয়ে যেতেন গৌতম, গোটা জগৎ শাসন করতে পারতেন। কত কিছু তিনি করতে পারবেন, ভাবুন। দয়ালু সরকারের সাহায্যে জীবনের দুঃখ-কষ্ট দূর করতে পারবেন তিনি। এটা অবশ্য একটা সহজ বিকল্প ও বিভ্রান্তি ছিল, কারণ শক্তি দিয়ে দুঃখকে জয় করা যায় না। এক অনালোকিত সত্তার প্রস্তাবনা ছিল এটা। গৌতমের সমগ্র জীবনে মারা তাঁর অগ্রগতি ব্যাহত করার প্রয়াস পাবেন, তাঁর মর্যাদা হ্রাসের প্রয়াসে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করবেন। সে রাতে গৌতম অনায়াসে মারার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ক্রুদ্ধ দেবতা হাল ছাড়তে রাজি হননি। ‘তোমাকে আমি ধরব,’ আপনমনে ফিসফিস করে বলেছেন তিনি, ‘যখনই তোমার মনে নোংরা, ঘৃণিত বা বাজে চিন্তা খেলে যাবে।’ মুহূর্তের দুর্বলতায় ফাঁদে ফেলার জন্যে গৌতমকে ‘চিরস্থায়ী ছায়ার মতো’ অনুসরণ করে গেছেন তিনি।[৪২] গৌতম পরম আলোকপ্রাপ্ত হওয়ার বহু পরেও মারার বিরুদ্ধে সতর্ক সজাগ থাকতে হয়েছে তাঁকে, সম্ভবত জাঙ্গীয় মনস্তাত্ত্বিকরা যাঁকে তাঁর ছায়া-সত্তা বলবেন, তিনি তাঁকে তুলে ধরছেন–যা আমাদের মুক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে চলা মনের সমস্ত অবচেতন উপাদান। আলোকপ্রাপ্তি কখনওই সহজ নয়। আমাদের পুরোনো সত্তাকে ত্যাগ করা ভীতিকর, কারণ কেমন করে বাঁচতে হয় সেটা জানার ওটাই আমাদের একমাত্র উপায়। অসন্তোষজনক হলেও আমরা পরিচিত জিনিস আঁকড়ে থাকতে চাই, কারণ আমরা অজানাকে ভয় পাই। কিন্তু গৌতমের বেছে নেওয়া পবিত্র জীবনের দাবি ছিল তিনি তাঁর ভালোবাসার সমস্ত কিছু ও তাঁর অপরিপক্ক ব্যক্তিত্বকে গঠনকারী সবকিছুকে ত্যাগ করবেন। প্রতিটি বাঁকে তিনি তাঁর ওই অংশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেছেন (মারার মাধ্যমে প্রতীকায়িত) যা এই সামগ্রিক আত্ম-পরিত্যাগে কুঁকড়ে গেছে। মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকবার সম্পূর্ণ ভিন্ন উপায়ের সন্ধান করছিলেন গৌতম এবং এই নতুন সত্তার জন্ম দেওয়ার জন্যে দীর্ঘমেয়াদী কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন হবে। দক্ষতারও প্রয়োজন হবে। আলোকপ্রাপ্তিতে সাহায্য করতে পারবেন এমন একজন গুরুর খোঁজে নামলেন গৌতম।
***
তথ্যসূত্র
১. গৌতমের জন্ম ও ‘অগ্রসর হওয়া’র তারিখ এখন বিতর্কিত। পশ্চিমা পণ্ডিতগণ এক সময় অনুমান করেছিলেন যে, ৫৬৩ সাল নাগাদ জন্ম গ্রহণ করেছেন তিনি। সুতরাং, সে অনুযায়ী ৫৩৪-এর দিকে গৃহত্যাগ করে থাকবেন। কিন্তু সাম্প্রতিক পণ্ডিতগণ আভাস দিয়েছেন, ৪৫০ বিসিই নাগাদ গৌতম গৃহত্যাগ করে থাকতে পারেন। হেইনয বারচ্যান্ট, ‘দ্য ডেইট অভ বুদ্ধ রিকনসিডারড’, ইন্দোলোজিয়া টরিনেনসিন, ১০।
২. গৌতমের ছেলের নাম ছিল রাহুলা, সাধারণভাবে যা ‘বাঁধন’ হিসাবে অনুবাদ করা হয়। কোনও কোনও আধুনিক পণ্ডিত এই উদ্ভাবনকে প্ৰশ্ন সাপেক্ষ মনে করেছেন।
৩. মাজহিমা নিকয়া ৩৬.১০০।
৪. প্রাগুক্ত, ২৬, ৩৬, ৮৫, ১০০।
৫. জাতকা, ১: ৬২
৬. ল্যুক ৯: ৫৭-৬২; ১৪: ২৫-২৭; ১৮: ২৮-৩০।
৭. মাজহিমা নিকয়া, ২৬।
৮. আঙুত্তারা নিকয়া, ৩: ৩৮।
৯. মির্চা এলিয়াদ, দ্য মিথ অভ দ্য ইটারনাল রিটার্ন অর কসমস অ্যান্ড হিস্ট্রি, (অনু. উইলার্ড জে. ট্রাস্ক) প্রিন্সটন. এন জে, ১৯৫৪।
১০. মাজহিমা নিকয়া, ২৬
১১. উদনা, ৮: ৩।
১২. সুত্তা-নিপাতা, ৩: ১।
১৩. কার্ল জেস্পারস, দ্য অরিজিন অ্যান্ড গোল অভ হিস্ট্রি, অনু. মাইকেল বুলক, লন্ডন ১৯৫৩।
১৪. প্রাগুক্ত, ২-১২।
১৫. প্রাগুক্ত, ৭, ১৩।
১৬. প্রাগুক্ত, ২৮-৪৬।
১৭. জেনেসিস ২-৩।
১৮. জোসেফ ক্যাম্পবেল, অরিয়েন্টাল মিথলোজি, দ্য মাস্কস্ অভ গড, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬২, ২১১-১৮।
১৯. বিনয়া: কুলাভাগ্য ৬: ৪; ৭: ১।
২০. মাজহিমা নিকয়া, ৪।
২১. আলফ্রেড ওয়েবার, কালচারজেশিকতে আলস কাল্পচারসাযিওলোজি, লেইডেন, ১৯৩৫; দাস ব্রাজিশচে আন্দ দাই জেসাচিশতে, হামবূৰ্গ, ১৯৪৩।
২২. রিচার্ড এফ, গমব্রিচ, থেরাভেদা বুদ্ধজম: আ সোশ্যাল হিস্ট্রি ফ্রম অ্যানেশেন্ট বেনারেস টু মডার্ন কলোম্বো, লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৮, ৩৩-৫৯।
২৩. প্রাগুক্ত, ৩৩-৩৪; হারমান অলদেনবার্গ, দ্য বুদ্ধা: হিজ লাইফ, হিজ ডকট্রিন, হিজ অর্ডার (অনু. উইলিয়াম হোয়ে), লন্ডন, ১৮৮২, ১৯-২১, ৪৪-৪৮: ট্রেভর লিঙ, দ্য বুদ্ধা: বুড্ডিস্ট সিভিলাইজেশন ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড সিলোন, লন্ডন, ১৯৭৩, ৬৬-৬৭।
২৪. সুকুমার দত্ত, বুড্ডিস্ট মঙ্কস অ্যান্ড মনেস্টারিজ অভ ইন্ডিয়া, লন্ডন, ১৯৬২, ৭৩।
২৫. জেস্পারস, অরিজিন অ্যান্ড গোল, ৪৮-৪৯।
২৬. প্রাগুক্ত, ৫৫।
২৭. মার্শাল জি.এস. হজসন, দ্য ভেঞ্চার অভ ইসলাম, কনশিয়েন্স অ্যান্ড হিস্ট্রি ইন আ ওঅর্ল্ড সিভিলাইজেশন, ৩ খণ্ড, শিকাগো ও লন্ডন, ১৯৭৪, ১০৮-৩৫।
২৮. লিঙ, দ্য বুদ্ধা, ৩৮-৫৫; মাইকেল কারিথার্স, দ্য বুদ্ধা, অক্সফোর্ড ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৩, ১৩-১৮; গমব্রিচ, থেরাভেদা বুদ্ধজম, ৫০-৫৯।
২৯. লিঙ, দ্য বুদ্ধা, ৪৮-৪৯।
৩০. গমব্রিচ, থেরাভেদা বুদ্ধজম, ৩৪৯-৫০; কারিথার্স, দ্য বুদ্ধা, ১২-১৪। ৩১. লিঙ, দ্য বুদ্ধা ৫৩-৬৩; মাইকেল এডোয়ার্ডস্, ইন দ্য ব্লোইং আউট অভ আ ফ্লেইম: দ্য ওঅর্ল্ড অভ দ্য বুদ্ধা অ্যান্ড দ্য ওঅর্ল্ড অভ ম্যান, লন্ডন, ১৯৭৬, ২৭-২৯।
৩২. রিচার্ড এফ. গমব্রিচ, হাউ বুদ্ধজম বিগান: দ্য কন্ডিশন্ড জেনেসিস অভ দ্য আর্লি টিচিংস, লন্ডন ও আটলান্টিক হাইল্যান্ডস্, এনজে. ১৯৯৬, ৩১-৩৩; থেরাভেদা বুদ্ধজম, ৪৬-৪৮; কারিথার্স, দ্য বুদ্ধা, ২৪-২৫; লিঙ, দ্য বুদ্ধা, ৪৭-৫২।
৩৩. লিঙ, দ্য বুদ্ধা, ৬৫-৬৬; অলদেনবার্গ, দ্য বুদ্ধা, ৪১-৪৪।
৩৪. চ্যান্দোগ্য উপনিষদ, ৬: ১৩।
৩৫. অলদেনবার্গ, দ্য বুদ্ধা, ৫৯-৬০।
৩৬. প্রাগুক্ত, ৬৪; ক্যাম্পবেল, অরিয়েন্টাল মিথলোজি: দ্য মাস্কস্ অভ গড, ১৯৭-৯৮।
৩৭. দত্ত, বুড্ডিস্ট মঙ্কস, ৩৮-৪০।
৩৮. জাতকা ১, ৫৪-৬৫, হেনরি ক্লার্ক ওয়ারেন’র বুদ্ধজম ইন ট্রান্সলেশন-এ, ক্যাম্ব্রিজ, ম্যাস, ১৯০০, ৪৮-৬৭।
৩৯. দিঘা নিকয়া ২: ২১-২৯।
৪০. জাতকা, ১: ৬১।
৪১. প্রাগুক্ত, ১: ৬৩।
২. অন্বেষণ
সূদূরবর্তী রাজ্য শাক্য পেছনে ফেলে মগধ রাজ্যে প্রবেশের পর নতুন সভ্যতার প্রাণকেন্দ্রে এসে পৌঁছেছিলেন গৌতম। পালি কিংবদন্তী আমাদের জানাচ্ছে, প্রথমে অল্প কিছুদিন মগধের রাজধানী অন্যতম শক্তিশালী উন্নয়নশীল নগর রাজাগহের বাইরে অবস্থান করেন তিনি। খাবার ভিক্ষা করার সময় আর কেউ নন, খোদ রাজা বিম্বিসারার নজরে পড়ে যান। তরুণ শাক্য ভিক্ষুকে দেখে এতই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি যে তাঁকে আপন উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করতে চেয়েছিলেন।[১] এটা স্পষ্টতই রাজাগহে গৌতমের প্রথম পদার্পণের কাল্পনিক অলঙ্করণ। তবে ঘটনাটি তাঁর ভবিষ্যৎ মিশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে। গৌতম ছিলেন কাপিলবাস্তুর নেতৃস্থানীয় পরিবারগুলোর একটির সদস্য, রাজা ও অভিজাতজনদের সঙ্গে অনায়াসে মিশতে পারতেন তিনি। শাক্যতে কোনও গোত্রপ্রথা ছিল না। কিন্তু সমাজের মূল স্রোতধারায় পৌঁছানোর পর নিজেকে ক্ষত্রিয় হিসাবে তুলে ধরেছেন তিনি সরকারের পক্ষে উপযোগি গোত্রের সদস্য। কিন্তু বহিরাগত কারও মতো বস্তুনিষ্ঠতা নিয়ে বৈদিক সমাজের কাঠামো পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছিলেন গৌতম। ব্রাহ্মণদের সমীহ করার জন্যে বড় করা হয়নি তাঁকে; কখনওই তাঁদের সঙ্গে সমস্যায় পড়েননি তিনি। পরে নিজস্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার পর তিনি উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে যে কোনও রকম কঠোর শ্রেণীবিন্যাসে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। এই সমালোচনামূলক অবস্থান শহরগুলোয় তাঁকে সুবিধাজনক অবস্থান দেবে যেখানে গোত্র-প্রথা ভেঙে পড়ছিল। গৌতমের প্রথম আহ্বানস্থল প্রত্যন্ত অঞ্চল না হয়ে বিরাট শিল্পনগরী হওয়ার বিষয়টি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কর্মজীবনের অধিকাংশ সময়ই শহর ও নগরে কাটাবেন তিনি, যেখানে নগরায়নের সঙ্গে আবির্ভূত পরিবর্তন ও উত্থানপতনের ফলে সৃষ্ট ব্যাপক অস্থিরতা ও বিস্ময়ের উপস্থিতি ছিল। পরিণামে বেশ আধ্যাত্মিক তৃষ্ণাও ছিল।
প্রথম দফার দীর্ঘ সময় রাজাগহে কাটাননি গৌতম, বরং তাঁর আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণে সাহায্য করতে পারবেন ও পবিত্র জীবনের প্রাথমিক বিষয়াদি শিক্ষা দিতে পারবেন এমন একজন গুরুর সন্ধানে নেমে পড়েছিলেন। শাক্যে গৌতম সম্ভবত গুটিকয় সন্ন্যাসীর দেখা পেয়েছিলেন। কিন্তু ওই অঞ্চলের শহরগুলোকে সংযুক্তকারী বাণিজ্যপথে নতুন অসংখ্য ভিক্ষুকে দেখে সম্ভবত হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। হয়তো শহরের বিভিন্ন বাড়ির দরজায় তাঁদের নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থাকবেন, সরাসরি খাবার না চেয়ে স্রেফ থালা সামনে বাড়িয়ে রেখেছেন। গৃহস্থরা তাদের উন্নত পুনর্জন্ম এনে দেবে এমন যোগ্যতা অর্জনে উদ্বিগ্ন থাকায় সাধারণত উচ্ছিষ্ট দিয়ে ওগুলো ভরে দিত। চাষাবাদের জমিকে ঘিরে রাখা বট, সেগুন ও নারিকেল গাছের জঙ্গলে ঘুমানোর জন্যে পথ ছেড়ে শিবিরে সন্ন্যাসীদের দল বেঁধে ঘুমোতে দেখে থাকবেন গৌতম। তাদের কেউ কেউ স্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে পবিত্র জীবনের সন্ধান করার সময় বনে-জঙ্গলে সংসার পেতেছেন। এমনকি ব্রাহ্মণরাও ছিলেন যাঁরা ‘মহান অনুসন্ধানে’ নামা সত্ত্বেও তিনটি পবিত্র অগ্নিকুণ্ডের পরিচর্যা করে কঠোরতর বৈদিক প্রেক্ষিতে আলোকপ্রাপ্তির প্রয়াস পাচ্ছিলেন। মধ্য-জুনে এলাকায় আঘাত হেনে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত থাকা বর্ষার বৃষ্টির কারণে ভ্রমণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে সন্ন্যাসীদের অনেকেই দলবেঁধে জঙ্গল বা শহরতলীর পার্ক ও শ্মশানে বাস করতেন যতক্ষণ না বানের পানি নেমে গিয়ে পথঘাট আবার সুগম হয়ে উঠত। গৌতম যখন তাঁদের দলে যোগ দিতে আসেন ততদিনে ভবঘুরে ভিক্ষুরা দৃশ্যপটের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিলেন। সমাজের একটা উল্লেখযোগ্য শক্তি ছিলেন তাঁরা। বণিকদের মতো তাঁরাও পঞ্চম গোত্রে পরিণত হয়েছিলেন।[২]
আগের দিনে অনেকেই সংসার ও নিয়মিত চাকরির একঘেয়ে পরিশ্রম থেকে নিস্তার পেতে এই বিশেষ আজিভা বৃত্তি বেছে নিয়েছিল। বরাবরই কিছু গৃহত্যাগী ছিল যারা মূলত ঘর-পালানো, দেনাদার, দেউলিয়া ও আইনের হাত থেকে পালিয়ে বেড়ানো লোকজন। কিন্তু গৌতম যখন অনুসন্ধান শুরু করেন তখন তাঁরা আরও সংগঠিত হয়ে উঠেছিলেন। এমনকি সবচেয়ে অঙ্গীকার বিহীন সন্ন্যাসীকেও তাদের অস্তিত্বের পক্ষে একটা আদর্শের প্রচার করতে হতো। ফলে বেশ কয়েকটা মতবাদের জন্ম হয়েছিল। কোসালা ও মগধের নতুন রাজ্যে সরকার অধিবাসীদের ওপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ আরোপ শুরু করেছিল। সামগ্রিকভাবে সমাজে অবদান রাখে না এমন কোনও বিকল্প জীবনধারা আঁকড়ে ধরতে জনগণকে অনুমতি দেয়নি। সন্ন্যাসীদের প্রমাণ করতে হয়েছে, তাঁরা পরজীবী নন, বরং দার্শনিক যাদের বিশ্বাস দেশের আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য উন্নতি ঘটাতে পারে।[৩]
অধিকাংশ নতুন আদর্শ পুনর্জন্ম ও কম্মের মতবাদ কেন্দ্রীক ছিল: তাদের লক্ষ্য ছিল ক্রমাগত এক অস্তিত্ব হতে আরেক অস্তিত্বে ঠেলে দেওয়া অন্তহীন সামসারা চক্র হতে নিস্তার লাভ। উপনিষদ শিক্ষা দিয়েছিল যে, দুঃখ-দুর্দশার প্রধান কারণ হচ্ছে অজ্ঞতা: অনুসন্ধানী একবার নিজের প্রকৃত ও পরম সত্তা (আত্মা)র গভীর জ্ঞান লাভ করার পর আবিষ্কার করবে যে আর আগের মতো তীব্রভাবে যন্ত্রণা বোধ করছে না, চূড়ান্ত মুক্তির আভাস লাভ করবে সে। কিন্তু মগধ, কোসালা ও গাঙ্গেয় সমতলের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সন্ন্যাসীগণ প্রায়োগিক বিষয়ে বেশি উৎসাহী ছিলেন। অজ্ঞতাকে দুঃখের প্রধান কারণ হিসাবে দেখার বদলে তাঁরা আকাঙ্ক্ষাকে (তানহা) আসল অপরাধী মনে করেছেন। আকাঙ্ক্ষা দিয়ে তাঁরা পবিত্র জীবনের সন্ধানে নামার মতো উৎসাহব্যঞ্জক আর উন্নতি সাধক কাজে অনুপ্রাণিতকারী সেইসব মহৎ ইচ্ছাকে বোঝাননি, বরং সেইসব কামনাকে বুঝিয়েছেন যা আমাদেরকে ‘আমি চাই,’ বলতে বাধ্য করে। তাঁরা নতুন সমাজের লোভ ও অহমবোধে ভারি উদ্বিগ্ন ছিলেন। আমরা যেমন দেখেছি, তাঁরা ছিলেন সময়ের সন্তান; রাজার এলাকায় আবির্ভূত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও আত্ম-নির্ভরতার রীতিনীতি আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু অ্যাক্সিয়াল-যুগের অন্য সাধুদের মতো জানতেন অহমবাদ বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়াতে পারে। পূর্ব-গাঙ্গেয় এলাকার সন্ন্যাসীদের বিশ্বাস ছিল যে এই পিপাসার্ত তানহাই মানুষকে সামসারায় আটকে রেখেছে। তাঁরা যুক্তি দেখিয়েছেন, আমাদের সকল কর্মকাণ্ড একটা পর্যায় পর্যন্ত আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত। আমরা একটা কিছু প্রয়োজন বোঝার পর সেটা পাওয়ার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিই: একজন পুরুষ যখন কোনও নারীকে কামনা করে, সে তাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করে; মানুষ প্রেমে পড়ে ভালোবাসার পাত্রকে অধিকার করতে চায়, আঁকড়ে ধরে আন্তরিকভাবে কাছে পেতে চায়। জাগতিক আরাম- আয়েস না চাইলে কেউই জীবিকা নির্বাহ করার জন্যে কঠোর ও প্রায়শঃ একঘেয়ে কাজ করতে যাবে না। সুতরাং আকাঙ্ক্ষা মানুষের কর্মকাণ্ডে (কম্ম ইন্ধন যোগায়। কিন্তু প্রতিটি কাজের দীর্ঘ মেয়াদী পরিণাম রয়েছে, সেটা ব্যক্তি পরবর্তী জীবনে যে অস্তিত্ব লাভ করবে তা নির্ধারণ করবে।
এটা বোঝায় যে, কম্ম পুনর্জন্মের দিকে চালিত করে। আমরা যদি আদৌ কোনও কাজ করা এড়িয়ে যেতে পারি, হয়তো পুনর্জন্মের দুঃখ আর পুনঃমৃত্যুর চক্র হতে নিজেদের মুক্ত করার সুযোগ পেতে পারি। কিন্তু আকাঙ্ক্ষা আমাদের কাজে বাধ্য করে। সুতরাং, উপসংহারে পৌঁছেছেন সন্ন্যাসীগণ আমরা আমাদের মন-প্রাণ থেকে তানহাকে নিশ্চিহ্ন করতে পারলে আমরা অল্প সংখ্যক কম্ম সম্পাদন করতে পারব। কিন্তু একজন গৃহস্থের নিজেকে আকাঙ্ক্ষা হতে মুক্ত করার কোনও সুযোগ নেই। তার গোটা জীবন একের পর এক সর্বনেশে কাজের সম্মিলন।[৪] বিবাহিত পুরুষ হিসাবে সন্তান জন্ম দেওয়া তার দায়িত্ব। কিছু পরিমাণ যৌন আকঙ্ক্ষা ছাড়া স্ত্রীর সঙ্গে ঘুমাতে পারবে না সে; কিছু পরিমাণ লোভ বাধ্য না করলে সাফল্য বা দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্পে নিয়োজিত হতে পারবে না। রাজা বা ক্ষত্রিয় হলে ক্ষমতার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া শাসন কাজে বা শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধেই লিপ্ত হতে পারবেন না। আসলেই তানহা ও তানহা হতে উদ্ভুত কাজ (কম্ম) ছাড়া সমাজ থমকে দাঁড়াত। একজন গৃহস্থের জীবন কামনা, লোভ ও উচ্চাভিলাষে প্রভাবিত হওয়ায় তাকে অস্তিত্বের মাঝে বন্দি করা কর্মকাণ্ডে বাধ্য করে: অনিবার্যভাবে সে আরেকটি যন্ত্রণাদায়ক জীবন সহ্য করার জন্যে জন্ম নেবে। সত্য বটে সৎ কৰ্ম্ম সম্পাদন করে যোগ্যতা অর্জন করতে পারে একজন গৃহস্থ। যেমন ভিক্ষুকে ভিক্ষা দিতে পারে এবং এভাবে ভবিষ্যতে কাজে আসার মতো মূল্য লাভ করতে পারে। কিন্তু সকল কৰ্ম্ম সীমাবদ্ধ বলে সেগুলোর পরিণামও সীমিত থাকবে, গৃহস্থকে নিব্বানার অপরিমেয় শান্তি এনে দিতে পারবে না। আমাদের কম্ম সবচেয়ে ভালো যেটা করতে পারে সেটা হলো পরবর্তী জীবনে আমরা কোনও স্বর্গীয় জগতে দেবতা রূপে জন্ম নিতে পারি। কিন্তু সেই স্বর্গীয় অস্তিত্বও একদিন শেষ হয়ে যাবে। পরিণামে একজন গৃহস্থের জীবনকে গড়ে তোলা অন্তহীন দায়িত্ব ও কর্তব্য সামসারা ও পবিত্রতা হতে বিচ্ছিন্নতার প্রতাঁকে পরিণত হয়েছে। এই পরম কর্মকাণ্ডের ঘানিতে আটকে পড়ে গৃহস্থের মুক্তির আর কোনও আশাই ছিল না।
কিন্তু সন্ন্যাসীর অবস্থান ছিল উন্নততর। তিনি যৌনতাকে বিসর্জন দিয়েছেন: ভরণপোষণ করার জন্যে তাঁর কোনও স্ত্রী-সন্তান নেই; কোনও কাজ বা ব্যবসায়ে নিয়োজিত হবার কোনও প্রয়োজন নেই তাঁর। গৃহস্থের তুলনায় মোটামুটি কর্মহীন জীবন উপভোগ করেন।[৫] কিন্তু সামান্য কম্ম সম্পাদন করলেও সন্ন্যাসী তাঁকে এই জীবনে আবদ্ধ করে রাখা আকাঙ্ক্ষা বোধ করেন। এমনকি সবচেয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ সন্ন্যাসীও জানেন, তিনি নিজেকে আকাঙ্ক্ষা হতে মুক্ত করতে পারেননি। এখনও তিনি কামনায় তাড়িত হন; এখনও জীবনের ছোটখাট সুখের জন্যে মাঝে মাঝে ইচ্ছা বোধ করেন। প্রকৃতপক্ষে বঞ্চনা অনেক সময় আকাঙ্ক্ষা বাড়িয়ে দেয়। কেমন করে একজন সন্ন্যাসী নিজেকে মুক্ত করতে পারবেন? কেমন করে তিনি তাঁর আপন সত্তায় প্রবেশাধিকার পাবেন এবং তাঁকে বস্তু জগৎ হতে মুক্ত করবেন? যেখানে তাঁর সর্বাত্মক প্রয়াস সত্ত্বেও এখনও নিজেকে পার্থিব বস্তুর জন্যে আকাঙ্ক্ষা করতে দেখছেন? প্রধান প্রধান সন্ন্যাস-মতবাদে ভিন্ন ভিন্ন সমাধান দেখা দিয়েছিল। জনৈক গুরু মতবাদ ও অনুশীলনের ব্যবস্থা হিসাবে একটা ধৰ্ম্ম গড়ে তুলেছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, এটা এইসব দুর্গম সমস্যা মোকাবিলা করতে পারবে। এরপর তিনি একদল শিষ্যকে সংগঠিত করে এমন কিছু যা সংঘ বা গণ (ধর্মে গোত্রীয় দলবদ্ধতা বোঝাতে প্রাচীন বৈদিক পরিভাষা) নামে পরিচিত সংগঠন গড়ে তুললেন। এইসব সংঘ আধুনিক ধর্মীয় গোষ্ঠীর মতো সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান ছিল না। তাদের সামান্য বা কোনওরকম সাদৃশ্যমূলক জীবন ধারা ছিল না, ছিল না কোনও আনুষ্ঠানিক আচরণ বিধিও। সদস্যরা ইচ্ছামতো যোগ দিত ও বিদায় নিত। আরও সুবিধাজনক ধৰ্ম্মের সন্ধান পাওয়ামাত্র সন্ন্যাসীকে গুরুকে ত্যাগে বিরত রাখার মতো কিছু ছিল না। সন্ন্যাসীরা সাধ্যমতো সেরা গুরুর সন্ধানে ঘুরে বেড়াতেন। পথে পরস্পরকে সম্ভাষণ জানানো ভিক্ষুদের রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল। তাঁরা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করতেন: ‘আপনার গুরু কে? আপনি কোন ধৰ্ম্ম পালন করেন?’
মগধ ও কোসালায় ভ্রমণের সময় স্বয়ং গৌতমও সম্ভবত এভাবে পাশ কাটানো সন্ন্যাসীদের প্রশ্ন করে থাকবেন, কারণ একজন গুরু ও সংঘের সন্ধানে ছিলেন তিনি। শুরুতে আদর্শের সংঘাত তাঁর কাছে বিভ্রান্তিকর মনে হয়ে থাকতে পারে। সংঘগুলো প্রতিযোগিতামূলক ছিল, বণিকরা যেভাবে বাজার এলাকায় নিজ নিজ পণ্য বিক্রি করত ঠিক সেরকম আগ্রাসীভাবে ধম্ম প্রচার করত তারা। অত্যুৎসাহী শিষ্যরা তাদের গুরুদের ‘বুদ্ধ’ (‘আলোকপ্রাপ্ত জন) ) বা ‘মানুষ ও দেবতাদের গুরু’ বলে সম্বোধন করেও থাকতেও পারে।[৬] অন্যান্য অ্যাক্সিয়াল দেশের মতো বিভিন্ন বিষয়ে জোরাল বিতর্ক, বেশ উন্নত যুক্তি ও জনগণের আগ্রহ ছিল। ধর্মীয় জীবন অল্প কিছু ধর্মান্ধের একচেটিয়া বিষয় নয় বরং সবার আগ্রহের বিষয় ছিল। নগর মিলনায়তনে গুরুরা পরস্পরের সঙ্গে বিতর্ক করতেন: জন-হিতোপদেশ শুনতে জড়ো হতো জনতা।[৭] সাধারণ মানুষ পক্ষ নিয়ে এক সংঘের বিরুদ্ধে অন্য সংঘকে সমর্থন যোগাত। কোনও এক সংঘের নেতা শহরে এলে গৃহস্থ, বণিক ও সরকারি কর্মকর্তরা তাকে খুঁজে বের করত। তাঁকে ধৰ্ম্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করত। আমরা আজকাল ফুটবল দল নিয়ে যেমন উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করি তেমন উৎসাহের সঙ্গে তার গুনাগুন আলোচনা করত। সাধারণ জনগণ এইসব বিতর্কের সূক্ষ্ম বিষয় বুঝতে পারত। কিন্তু তাত্ত্বিক বিষয়ে কখনও আগ্রহ ছিল না তাদের। ভারতে ধর্মীয় জ্ঞানের একটা মানদণ্ড ছিল: এটা কি ফলদায়ক? এটা কি ব্যক্তিকে বদলে দেবে, জীবন-যন্ত্রণা দূর করবে, শান্তি ও চূড়ান্ত মুক্তির আশা যোগাবে? কেউই খামোকা অধিবিদ্যিক মতবাদে আগ্রহী ছিল না। ধম্মের বাস্তবমুখীতা থাকার প্রয়োজন ছিল: উদাহরণ স্বরূপ, বনচারী সন্ন্যাসীদের প্রায় সকল আদৰ্শই নয়া সমাজের আগ্রাসন ঠেকাতে চেয়েছে, সৌজন্য ও অমায়িকতার পক্ষে অহিংসার নীতি তুলে ধরেছে।
এভাবে মাক্কালি, গোসালা ও পুরানা কশ্যাপা গুরুদের অনুসরণকারী অজিভাকাস কম্মের চলমান ধারণা অস্বীকার করেছেন: হাজার বছর সময় লাগলেও শেষ পর্যন্ত সবাইই সামসারা হতে মুক্তি লাভ করবে বলে তাঁরা বিশ্বাস করতেন। প্রত্যেককে নির্দিষ্ট সংখ্যক জীবন যাপন করতে হবে। সব ধরনের জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হবে। মনের শান্তির বিকাশ ঘটানোই ছিল এই ধম্মের মূল কথা। ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনও কারণ নেই, কেননা সমস্ত কিছুই পূর্ব-নির্ধারিত। মোটামুটি একই চেতনায় অমিতের নেতৃত্বাধীন বস্তুবাদীরা পুনর্জন্ম মতবাদ অস্বীকার করেন। তাঁদের যুক্তি, মানুষ সম্পূর্ণ ভৌত সৃষ্টি বলে স্রেফ মৃত্যুর পর আবার মূল উপাদানে ফিরে যাবে। সুতরাং আপনি যেমন আচরণ করেন না কেন তার কোনওই গুরুত্ব নেই, কারণ সবার জন্যে একই নিয়তি অপেক্ষা করছে। তবে যার যেমন ইচ্ছা তেমন করে শুভেচ্ছা ও সুখীভাব লালন করা এবং সেইসব কম্ম সম্পাদনই সম্ভবত মঙ্গলজনক যেগুলো এই উদ্দেশ্য পূরণ করে। সংশয়বাদীদের নেতা সঞ্জয় যে কোনও রকম চূড়ান্ত সত্যের সম্ভাবনা অস্বীকার করেছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যে, সকল কম্মের উদ্দেশ্য উত্তয়া উচিত বন্ধুত্ব ও মনের শান্তি বিকশিত করা। সকল সত্যই যেহেতু আপেক্ষিক, আলোচনা কেবল তিক্ততারই সৃষ্টি করবে। সুতরাং এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। গৌতমের জীবদ্দশায়ই মহাবীর নামে পরিচিত বর্ধমান জ্ঞানপুত্রের নেতৃত্বাধীন জৈনরা বিশ্বাস করত যে, অশুভ কৰ্ম্ম আত্মাকে সূক্ষ্ম ধূলোয় ঢেকে দেয়। ফলে আত্মা ভারি হয়ে নিম্নগামী হয়। কেউ কেউ তাই যেকোনও ধরনের কম্ম এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করত। বিশেষ করে সেই ধরনের কম্ম যেগুলো অন্য কোনও প্রাণীর ক্ষতি করতে পারে-এমনকি গাছ বা কীট পতঙ্গও। অজান্তে কোনও কাঠিতে পা দিয়ে ফেলতে পারে বা এক ফোঁটা পানি ফেলে দেবে, এই ভয়ে জৈনদের কেউ কেউ নিশ্চল থাকার প্রয়াস পেয়েছে। কেননা জীবনের এই নিম্ন পর্যায়ের ধরণগুলোর সবই প্রাণ ধারণ করে; পূর্বজন্মের অসৎ কম্মের কারণে আটকা পড়ে গেছে। কিন্তু জৈনরা প্রায়শঃই এই অসাধারণ কোমলতার সঙ্গে নিজেদের বিরুদ্ধে সহিংসতার মিশ্রণ ঘটিয়েছে। অসৎ কম্মের প্রভাব দূর করতে ভয়ঙ্কর প্রায়শ্চিত্তের আশ্রয় নিয়েছে: উপবাস পালন করত তারা, পান বা স্নানে অস্বীকৃতি জানাত আর প্রচণ্ড গরম বা শীতে নিজেদের উন্মুক্ত করতে চাইত না।[৮]
এইসব সংঘের কোনওটায়ই যোগ দেননি গৌতম। বরং সমক্ষ্যের একটা ধরনের শিক্ষা দানকারী আলারা কালামের ধম্মে দীক্ষা নেওয়ার জন্যে বিদেহা রাজ্যের রাজধানী বেসালির মহল্লায় চলে গেছেন।[৯] গৌতম সম্ভবত আগে হতেই সমক্ষ্য দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে থাকবেন, কেননা এই সমক্ষ্য দর্শন (পার্থক্যকরণ) সবার আগে সপ্তম-শতাব্দীর গুরু কাপিলাই শিক্ষা দিয়েছিলেন কাপিলবাস্তুর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল তাঁর। এই মতবাদের বিশ্বাস ছিল, আকাঙ্ক্ষা নয়, বরং অজ্ঞতাই আমাদের সব সমস্যার মূল: প্রকৃত সত্তাকে বোঝার অক্ষমতা থেকেই আমাদের দুঃখ-দুর্দশার উদ্ভব। আমরা এই সত্তাকে সাধারণ মনস্তাত্ত্বিক জীবনের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলি। কিন্তু মুক্তি অর্জনের স্বার্থে আমাদের এক গভীর স্তরে সচেতন হয়ে উঠতে হবে যে সত্তার সঙ্গে এইসব ক্ষণস্থায়ী, সীমিত ও অসন্তোষজনক মানসিক অবস্থার কোনও সম্পর্ক নেই। সত্তা পরম আত্মা (পুরুসা)-র হুবহু অনুরূপ ও চিরন্তন, যা সমস্ত বস্তু ও প্রাণীতে প্রভাবশালী কিন্তু প্রকৃতির বস্তুজগৎ (প্রকৃতি) দিয়ে আড়াল করা। সমক্ষ্য দর্শন অনুসায়ী পবিত্র জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে প্রকৃতি হতে পুরুসার পার্থক্য করতে শেখা। নবীশকে আবেগের বিভ্রান্তি হতে ঊর্ধ্বে জীবন যাপন করা শিখতে হতো এবং মানুষের নিখুঁততম অংশ বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটাতে হতো, যার চিরন্তন আত্মার প্রতিফলন ঘটানোর ক্ষমতা রয়েছে, ঠিক যেভাবে আয়নায় ফুলের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। কোনও সহজ প্রক্রিয়া ছিল না এটা। কিন্তু একজন সন্ন্যাসী সত্যিকার অর্থে তাঁর প্রকৃত সত্তা মুক্ত, পরম ও চিরন্তন এ বিষয়ে সচেতন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মুক্তি অর্জন করতেন। অন্যতম ধ্রুপদী টেক্সটে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, প্রকৃতি তখন নিমেষে ‘গুরুর ইচ্ছা পূরণের পর কোনও নৃত্যশিল্পীর বিদায় নেওয়া’র মতো সত্তা হতে বিদায় নেবে।[১০] এই ব্যাপারটি ঘটে যাওয়ার পর সন্ন্যাসী আলোকপ্রাপ্ত হবেন, কারণ তিনি তাঁর প্রকৃত সত্তায় জাগ্রত হয়েছেন। দুঃখ-দুর্দশা তাঁকে আর স্পর্শ করতে পারবে না, কেননা তিনি জানেন তিনি চিরন্তন, পরম। প্রকৃতপক্ষেই নিজেকে তিনি ‘আমি কষ্ট পাচ্ছি’র বদলে ‘ওটা কষ্ট পাচ্ছে,’ উচ্চারণ করতে শুনবেন, কারণ এখন যাকে তাঁর প্রকৃত পরিচয় হিসাবে জানেন যন্ত্রণা তার বহু দূরের অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়েছে। আলোকপ্রাপ্ত সাধু পৃথিবীতে বাস করে চলবেন এবং সম্পাদিত অসৎ কম্মের অবশিষ্টাংশ ভস্মীভূত করবেন, কিন্তু মারা যাবার পর আর পুনর্জন্ম নেবেন না, কেননা তিনি বস্তুগত প্রকৃতি হতে মুক্তি অর্জন করেছেন।[১১]
সমক্ষ্য দর্শন গৌতমের চোখে উপযোগি ঠেকেছে। আপন ধৰ্ম্ম নির্মাণের সময় এই দর্শনের কিছু উপাদান অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন তিনি। গৌতমের মতো একজনের কাছে স্পষ্টতই আকর্ষণীয় আদর্শ ছিল এটা, অতি সম্প্রতি জগতের মোহমুক্ত ঘটেছিল তাঁর, সর্বত্র পবিত্রতার সন্ধান করারই শিক্ষা দিয়েছিল এই আদর্শ। প্রকৃতি স্রেফ ক্ষণস্থায়ী বিষয়। একে যত নিপীড়ক মনে হোক না কেন, আদৌ চূড়ান্ত বাস্তবতা নয়, যাদের কাছে জগৎ অচেনা জায়গায় পরিণত হয়েছে সমক্ষ্য তাদের কাছে উপশমকারী দর্শন ছিল, কারণ এর শিক্ষা ছিল নৈরাশ্যজনক বাহ্যিক রূপ সত্ত্বেও প্রকৃতি আমাদের বন্ধু। আলোকপ্ৰাপ্তিতে মানুষকে তা সাহায্য করতে পারে। নারী-পুরুষের মতো প্রকৃতির জগতের প্রতিটি প্রাণী সত্তাকে মুক্ত করার তাগিদে চালিত হয়: প্রকৃতি এভাবে সত্তাকে মুক্ত হবার সুযোগ করে দিতে নিজেকে অতিক্রম করে যেতে বদ্ধপরিকর। এমনকি ভোগান্তিরও একটা পরিত্রাণমূলক ভূমিকা আছে, কারণ আমরা যতই কষ্ট ভোগ করি ততই এ জাতীয় কষ্ট হতে মুক্ত অস্তিত্বের কামনা করি। আমরা যতই প্রাকৃতিক জগতের সমস্যা মোকাবিলা করি ততই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করি। আমরা যতই বুঝতে পারি যে, আমাদের জীবন বাহ্যিক শক্তি দিয়ে নিয়ন্ত্রিত আমরা ততই পুরুসার পরম, নিয়ন্ত্রণহীন সত্তার আকাঙ্ক্ষা বোধ করি। কিন্তু আকাঙ্ক্ষাটুকু যত শক্তিশালী হোক না কেন, প্রায়শঃই একজন সাধু বস্তুজগৎ হতে নিজেকে মুক্ত করা কঠিন আবিষ্কার করেন। মরণশীল মানুষ আবেগের ঝঞ্ছাবিক্ষুব্ধ জীবন ও দেহের উচ্ছৃঙ্খল জীবনের ঊর্ধ্বে উঠে কেবল বুদ্ধিমত্তার উপর নির্ভর করে বাঁচবে?
অচিরেই এই সমস্যার মুখোমুখি হলেন গৌতম। তিনি আবিষ্কার করলেন, সমক্ষ্যের সত্য সাধনা প্রকৃত মুক্তি বয়ে আনেনি। কিন্তু প্রথমে দীর্ঘপথ পেরিয়ে যান তিনি। আলারা কালাম শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করেন তাঁকে এবং প্রতিশ্রুতি দেন যে অচিরেই তিনি ধম্ম উপলব্ধি করতে পারবেন, গুরুর সমান জ্ঞান অর্জন করতে পারবেন। এই মতবাদ আপন করে নেবেন। অল্প দিনেই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো আত্মস্থ করে নিলেন গৌতম। অচিরেই সংঘের অন্যান্য সদস্যের মতোই অনর্গল গুরুর শিক্ষা আবৃত্তি করতে শিখে গেলেন। কিন্তু আশ্বস্ত হতে পারলেন না। কিছু একটা ঘাটতি রয়েছে। আলারা কালাম প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এইসব শিক্ষা ‘উপলব্ধি’ করতে পারবেন তিনি, সেগুলোর সম্পর্কে ‘প্রত্যক্ষ জ্ঞান’ অর্জন করবেন। সেসব আর বাহ্যিক সত্য হিসাবে রয়ে যাবে না বরং তার আপন সত্তার সঙ্গে মিশে গিয়ে জীবনের বাস্তবতায় পরিণত হবে। অচিরেই তিনি ধম্মের একজন জ্বলন্ত মূর্ত প্রকাশ হয়ে উঠবেন। কিন্তু তেমন কিছু ঘটছিল না। তিনি আলারা কালামের ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক মতবাদে ‘প্রবেশ করে’ তাতে ‘বসবাস’ করছেন না, শিক্ষা দূরবর্তী রয়ে গেছে। শিক্ষা অধিবিদ্যিক দূরবর্তী বিমূর্ত বিষয় রয়ে গেছে, তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সামান্যই সম্পর্ক আছে মনে হয়েছে। সর্বাত্মক প্রয়াস সত্ত্বেও প্রকৃত সত্তার কোনও আভাস পেলেন না তিনি। প্রকৃতির দুর্ভেদ্য আচ্ছাদনে একগুঁয়ের মতো আড়ালে রয়ে গেছে। এটা খুবই সাধারণ ধর্মীয় প্রতিবন্ধকতা। মানুষ প্রায়শঃই অন্যের সাক্ষ্য মেনে নিয়ে কোনও ঐতিহ্যের সত্যকে বিশ্বাস করে নেয়। কিন্তু দেখে যে, ধর্মের সারৎসার, আলোকময় সত্তা আড়ালে রয়ে গেছে। কিন্তু এই পথে চলার মতো অবকাশ গৌতমের ছিল না। কখনওই কোনও কিছু আপসে মেনে নেননি তিনি। পরে তাঁর নিজস্ব সংঘ গঠনের পর শিষ্যদের লাগাতার যে কোনও রকম জনশ্রুতিকে নির্বিচারে মেনে নিতে নিষেধ করেছেন। তারা যেন গুরুর সমস্ত কথাই বিনা সমালোচনায় মেনে না নেয়। বরং প্রত্যেক ক্ষেত্রে ধম্মকে যাচাই করে, নিজস্ব অভিজ্ঞতায় অনুরণিত হচ্ছে কিনা সেটা নিশ্চিত করে।
তো অনুসন্ধানের এই প্রাথমিক পর্যায়েও আলারা কালামের ধম্মকে বিশ্বাস হিসাবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন তিনি। গুরুর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কীভাবে এইসব মতবাদ ‘উপলব্ধি’ করতে পেরেছেন তিনিঃ নিশ্চয়ই স্রেফ অন্য কারও কথা মেনে নেননি? আলারা কালাম স্বীকার গেলেন, তিনি তাঁর সমক্ষ্য দর্শনের ‘প্রত্যক্ষ্য জ্ঞান’ কেবল ধ্যানের মাধ্যমে অর্জন করেননি। স্রেফ স্বাভাবিক যৌক্তিক চিন্তাভাবনা দিয়ে এইসব মতবাদের ভেতর প্রবেশ করেননি তিনি। যোগের অনুশীলন করেছেন।[১২]
যোগ সাধনা কবে ভারতে বিকাশ লাভ করেছিল আমরা জানি না।[১৩] আর্য গোত্রগুলো উপমহাদেশে আগ্রাসন চালানোর আগেও এখানে যোগের কোনও কোনও ধরনের অনুশীলন হয়ে থাকতে পারে এমন আলামত আছে। বিসিই দ্বিতীয় সহস্রাব্দের সময়কার মোহর পাওয়া গেছে যেখানে যোগাসনের মতো ভঙ্গিতে আসীন মানুষের চিত্র রয়েছে। গৌতমের জীবনকালের বেশ পরেই কেবল যোগের উপর লিখিত বিবরণ দেখা যায়। ধ্রুপদী টেক্সট লিখিত হয়েছে সিই দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতকে। বিসিই দ্বিতীয় শতাব্দীর অতিন্দ্রীয়বাদী পতঞ্জলির শিক্ষার ভিত্তিতে এসব রচিত। পতঞ্জলির ধ্যান ও মনোসংযোগের পদ্ধতি সমক্ষ্যের দর্শন ভিত্তিক হলেও সমক্ষ্যের বিভক্তির পর্যায়েই তার সূচনা। কোনও অধিবিদ্যিক তত্ত্ব তুলে ধরা নয় বরং সচেতনতার একটা ভিন্ন ধরনের বিকাশই তাঁর লক্ষ্য ছিল, যা সত্যিই আমাদের ইন্দ্রীয়াতীত সত্যে প্রবেশ করাতে পারবে। এখানে মনস্তাত্বিক ও শারীরিক কৌশলের মাধ্যমে স্বাভাবিক চেতনাবোধ অতিক্রম করে যাওয়ার প্রয়োজন, যোগিকে যা অতিন্দ্রীয় ও যুক্তির অতীত অর্ন্তদৃষ্টি দান করবে। আলারা কালামের মতো পতঞ্জলিও জানতেন, আঁচ অনুমান ও ধ্যান সত্তাকে প্রকৃতি থেকে মুক্ত করতে পারে নাঃ সম্পূর্ণ শক্তি দিয়ে যোগিকে এটা অর্জন করতে হয়। বাস্তবতাকে উপলব্ধি করার সাধারণ পথ ধ্বংস করতে হয় তাকে, স্বাভাবিক চিন্তা-প্রক্রিয়াকে আড়াল করে, আপন জাগতিক (নিম্ন পর্যায়ের) সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে অনীহ, অবাধ্য মনকে বল প্রয়োগ করে এমন একটা স্তরে নিয়ে যেতে হয় যেখানে ভ্রান্তি ও বিভ্রমের স্থান নেই। কিন্তু যোগে অতিপ্রাকৃত বলে কিছু নেই। পতঞ্জলি বিশ্বাস করতেন, যোগি স্রেফ তার মনস্তাত্ত্বিক ও মানসিক শক্তিকে ব্যবহার করছে। পতঞ্জলী বুদ্ধের মৃত্যুর বহু পরে শিক্ষা দিচ্ছিলেন যদিও, কিন্তু এটা স্পষ্ট যে প্রায়শঃ সমক্ষ্যের দর্শনের সঙ্গে সম্পর্কিত যোগানুশীলন গৌতমের জীবদ্দশায় গাঙ্গেয় অঞ্চলে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল এবং বনচারী সন্ন্যাসীদের মাঝে জনপ্রিয় ছিল। গৌতমের আলোকপ্রাপ্তিতে যোগ গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে। নিজস্ব ধৰ্ম্ম বিকাশে তিনি তিনি এই ঐতিহ্যবাহী অনুশীলন গ্রহণ করেন। সুতরাং, এই ঐতিহ্যবাহী যোগ পদ্ধতি অনুধাবন করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যা গৌতম সম্ভবত আলারা কালামের কাছে শিখেছিলেন এবং যা তাঁকে নিব্বানের পথে নিয়ে গিয়েছিল।
‘যোগ’ শব্দটি ক্রিয়াপদ ইউজ: ‘জোয়াল পরানো’ বা ‘একত্রে গ্রন্থিত করা’ হতে নেওয়া।[১৪] এর লক্ষ্য যোগির মনকে তার সত্তার সঙ্গে সংযুক্ত করা ও মনের সকল শক্তি ও প্রণোদনাকে গ্রন্থিত করা যাতে সকল চেতনা এমনভাবে ঐক্যবদ্ধ হয় যা সাধারণভাবে মানুষের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের মন সহজেই বিচ্যুত হয়। কোনও একটা বিষয়ে দীর্ঘ সময় মনোসংযোগ প্রায়ই কঠিন। এমনকি সবচেয়ে অনুপযুক্ত মুহূর্তেও মনের গহনে অনাহুত চিন্তা ও কল্পনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যেন। এইসব অবচেতন প্রণোদনার ওপর আমাদের যেন তেমন কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। মানসিক কর্মকাণ্ডের অনেকটাই স্বয়ংক্রিয়: একটা দৃশ্য আরেকটিকে ডেকে আনে; দীর্ঘ বিস্মৃতি হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কে স্পন্দিত হয়। বিরল ক্ষেত্রে আমরা কোনও বস্তু বা ধারণাকে সেটার স্বরূপে বিবেচনা করি, কারণ তা ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে যা তাকে অচিরেই বিকৃত করে। সেটাকে বস্তুগতভাবে বিবেচনা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব করে তোলে। এইসব মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার কিছু কিছু যন্ত্রণায় পরিপূর্ণ: এগুলো অজ্ঞতা, অহমবোধ, আবেগ, বিতৃষ্ণা ও আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি দিয়ে বৈশিষ্ট্যায়িত হয়, অবচেতন কর্মকাণ্ডে (বাসনা) প্রোথিত বলে এগুলো শক্তিশালী, নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন; কিন্তু আমাদের আচরণে এসবের গভীর প্রভাব রয়েছে। ফ্রয়েড ও জাং আধুনিক সাইকোঅ্যানালিসিস পদ্ধতি গড়ে তোলার বহু আগে ভারতীয় যোগিরা অবচেতন মন আবিষ্কার করে কিছু মাত্রায় তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছিল। সুতরাং যোগ গভীরভাবে অ্যাক্সিয়াল যুগের রীতির সঙ্গে সম্পর্কিত–মানুষকে নিজের সম্পর্কে অধিকতর পূর্ণাঙ্গভাবে সচেতন করে তোলা এবং অস্পষ্টভাবে অনুভূত বিষয়কে প্রকাশ্য আলোয় তুলে আনাই এর প্রয়াস। অনুশীলনকারীর আধ্যাত্মিক অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে থাকলে তা এইসব অবাধ্য বাসনাকে শনাক্ত করে পরিত্রাণে সক্ষম করে তোলে। কঠিন ছিল এই প্রক্রিয়া। প্রতিটি ধাপে যোগির একজন গুরুর সযত্ন তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন হতো, ঠিক আধুনিক অ্যানালিস্যান্ডের যেমন একজন অ্যানালিস্টের সহায়তার প্রয়োজন হয়। অবচেতন মনের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করার জন্যে যোগিকে স্বাভাবিক জগতের সঙ্গে সাধারণ সম্পর্ক ছিন্ন করতে হতো। প্রথমত, যে কোনও সন্ন্যাসীর মতোই সমাজ পেছনে ফেলে ‘পথে নামতে’ হতো তাকে। তারপর কঠোর নিয়ম পালনের প্রয়োজন হতো, যা তাকে ধাপে ধাপে সাধারণ আবরণ ও মনের স্বভাবের বাইরে নিয়ে যেত। পুরোনো সত্তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে সে প্রকৃত সত্তাকে–সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সত্তা-জাগিয়ে তুলবে বলে আশা করা হতো।
কোনও কোনও পশ্চিমার কাছে এসব যারপরনাই অদ্ভুত ঠেকতে পারে, যোগ সম্পর্কে যাদের সম্পূর্ণ ভিন্নরকম অভিজ্ঞতা রয়েছে। অ্যাক্সিয়াল যুগের সাধু ও পয়গম্বরগণ ক্রমশঃ উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন যে, অহমবাদ তাঁরা যে পরম ও পবিত্র সত্তার সন্ধান করছেন তাঁর দেখা পাওয়ার পথে সবচেয়ে বড় বাধা। ঈশ্বর, ব্রাহ্মণ বা নিব্বানের সত্তাকে বুঝতে হলে নারী বা পুরুষকে আমাদের মানবীয় অবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত মনে হওয়া স্বার্থপরতাকে বিসর্জন দিতে হবে। চীনা দার্শনিকগণ শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, মানুষ আলোকপ্রাপ্ত হতে চাইলে তাকে অবশ্যই তার আকাঙ্ক্ষা ও আচরণকে জীবনের অত্যাবশ্যকীয় ছন্দে সমর্পণ করতে হবে। হিব্রু পয়গম্বরগণ ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণের কথা বলেছেন। পরবর্তীকালে জেসাস তাঁর শিষ্যদের জানাবেন যে, আধ্যাত্মিক সন্ধান সত্তায় মৃত্যুবরণ দাবি করে: একটি গমের বীজকে তার পূর্ণ সম্ভাবনা অর্জন ও ফল ধারণ করার জন্যে আগে মাটিতে ঝরে পড়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে। মুহাম্মদ (স) ইসলামের গুরুত্ব প্রচার করবেন: ঈশ্বরের কাছে সমগ্র সত্তার আত্মসমর্পণ। আমরা যেমন দেখব, স্বার্থপরতা ও অহমবাদের বিসর্জন গৌতমের নিজস্ব ধৰ্ম্মের মুলকথা হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু ভারতীয় যোগিরা ইতিমধ্যেই এর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিল। যোগকে জগৎ সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে বিকৃতকারী ও আমাদের আধ্যাত্মিক অগ্রগতিতে বাধা দানকারী অহমবাদের সুশৃঙ্খল ধ্বংস হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। বর্তমানে আমেরিকা ও ইউরোপে যারা যোগ চর্চা করেন তারা সব সময় এই উদ্দেশ্য অনুসরণ করেন না। তারা প্রায়শঃ স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানোর লক্ষ্যে যোগের অনুশীলনকে কাজে লাগান। দেখা গেছে, মনোসংযোগের এইসব অনুশীলন মানুষকে অতিরিক্ত উদ্বেগ দমন বা দূর করতে সাহায্য করে। অনেক সময় ক্যান্সার রোগিরা আধ্যাত্মিক ভাবাবেশ অর্জনের জন্যে যোগিদের ব্যবহৃত মনোছবি কৌশল কাজে লাগান; আক্রান্ত কোষকে কল্পনা করার প্রয়াস পান তারা, রোগের বিস্তারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে অবচেতন শক্তিসমূহ জাগিয়ে তুলতে চান। সঠিকভাবে চর্চা করলে যোগ অনুশীলন নিঃসন্দেহে আমাদের নিয়ন্ত্রণ ও প্রশান্তি বাড়িয়ে তুলতে পারে। কিন্তু আদি যোগিগণ ভালো বোধ ও স্বাভাবিক জীবন যাপন করার লক্ষ্যে এই পথের যাত্রী হয়নি। তারা স্বাভাবিকতা ধ্বংস করে জাগতিক সত্তা মুছে ফেলতে চেয়েছে।
গৌতমের মতো গাঙ্গেয় সমতলের বহু সন্ন্যাসী বুঝতে পেরেছিলেন, যৌক্তিক অসংলগ্ন উপায়ে ধম্মের অনুধাবন দিয়ে কাঙ্ক্ষিত মুক্তি অর্জন করতে পারবেন না তাঁরা। চিন্তার যৌক্তিক ধরন মনের ছোট্ট একটি অংশকে কাজে লাগায়। আধ্যাত্মিক বিষয়েই কেবল চালিত করার প্রয়াস পেলে দেখা গেছে নিজেরই তার বিশৃঙ্খল জীবন রয়েছে। তারা দেখেছেন, মনোসংযোগের জন্যে যত জোরাল প্রয়াসই পান না কেন, অবিরাম অগুনতি বিক্ষিপ্ততা ও চেতনায় আক্রমণ চালানো অসহযোগি সম্পর্কের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেন তারা। কোনও ধম্মের শিক্ষাসমূহ প্রয়োগ শুরু করার পর নিজেদের মধ্যেই সব ধরনের নিয়ন্ত্রণাতীত মনে হওয়া প্রতিবন্ধকতা আবিষ্কার করেছেন তাঁরা। ইচ্ছাশক্তি যত জোরালই হোক না কেন, সত্তার কোনও গোপন অংশ নিষিদ্ধ বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে যায়। মনের মাঝে যেন সুপ্ত প্রবণতা রয়েছে যা আলোকনের বিরুদ্ধে বিকৃতরূপে সংঘাতে লিপ্ত হয়। যে শক্তিকে বৌদ্ধ টেক্টটসমূহ মারার পবিত্র ব্যক্তি রূপ দিয়েছে। অনেক সময় এইসব অবচেতন-প্রবণতা সন্ন্যাসীরা যুক্তির বয়সে পৌঁছার আগেই তাঁদের মাঝে রোপিত বা তাঁদের বংশগতির উত্তরাধিকারের অতীত অবস্থার ফলাফল। গাঙ্গেয় সন্ন্যাসীগণ অবশ্যই জিন সম্পর্কে কিছু বলেননি। তাঁরা ওই বাধার জন্যে বিগত জন্মের অসৎ কৰ্ম্মকে দায়ী করেছেন। কিন্তু কীভাবে তাঁরা তাঁদের বিশ্বাস অনুযায়ী মানসিক আলোড়নের অতীত চরম সত্তায় পৌঁছাতে এই অবস্থাকে পেরিয়ে যেতে পারবেন? কেমন করে উন্মত্ত প্রকৃতি থেকে সত্তাকে উদ্ধার করবেন?
বর্তমানে পশ্চিমে যে মুক্তির সন্ধান করা হয় তার চেয়ে অনেক মৌলিক, সাধারণত নিজেদের সীমাবদ্ধতার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝায় সন্ন্যাসীরা এমন স্বাভাবিক চেতনার পক্ষে অসম্ভব এক মুক্তির সন্ধান করেছেন। ভারতের সাধুরা মানবীয় ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণকারী শর্তাবলী হতে মুক্তি পেতে চেয়েছেন। আমাদের উপলব্ধিকে সীমিতকারী সময় ও স্থানের বাধাকে বাতিল করতে চেয়েছেন। তাঁদের কাঙ্ক্ষিত মুক্তি সম্ভবত সেইন্ট পল পরে যাকে “ঈশ্বর পুত্রদের মুক্তি’[১৫] বলে উল্লেখ করবেন তার কাছাকাছি। কিন্তু তাঁরা সেটা স্বর্গীয় জগতে প্রত্যক্ষ করার জন্যে আলাদা করতে রাজি ছিলেন না। নিজস্ব প্রয়াসে বর্তমানেই তাঁরা সেটা অর্জন করবেন। আলোকনের পথে অবচেতনবাদ অপসারণ ও মানবীয় ব্যক্তিত্বকে নিয়ন্ত্রণমুক্ত করার লক্ষ্যে যোগ সাধনার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। যোগিদের বিশ্বাস ছিল, একবার সেটা করা গেলে শেষপর্যন্ত তারা তাদের অনিয়ন্ত্রিত, চিরন্তন এবং পরম প্রকৃত সত্তার সঙ্গে একীভূত হয়ে যাবে।
সুতরাং সত্তাই ছিল অস্তিত্বের পবিত্র মাত্রার মূল প্রতীক, একেশ্বরবাদের ঈশ্বর, হিন্দুধর্মমতের ব্রাহ্মণ/আত্মা ও প্লেটোর দর্শনের শুভের মতো একই ভূমিকা পালন করেছে। গৌতম আলারা কালামের ধম্মে ‘বাস’ করার প্রয়াস পাওয়ার সময় এমন এক শান্তি আর সমগ্রতায় প্রবেশ ও বাস করতে চেয়েছিলেন যা জেনেসিস অনুযায়ী আদি মানব স্বর্গোদ্যানে প্রত্যক্ষ করেছিল। এই স্বর্গীয় শান্তি, এই শালোম, এই নিব্বানা ধারণাগতভাবে লাভ করাই যথেষ্ট ছিল না। তিনি সেই ‘প্রত্যক্ষ জ্ঞান’ চেয়েছিলেন যা তাঁকে আমাদের বসবাসের, শ্বাস-প্রশ্বাসের ভৌত পরিবেশের মতো আবৃত করে ফেলবে। তাঁর বিশ্বাস ছিল, তিনি তাঁর মনের গভীরে এই দুর্ভেয় ছন্দের অনুভূতি লাভ করবেন। তাকে পুরোপুরি পাল্টে দেবে সেটা: এক নতুন সত্তা অর্জন করবেন তিনি যা আর রক্ত মাংসের উত্তরাধিকার সেই যন্ত্রণার শিকারে পরিণত হবে না। সকল অ্যাক্সিয়াল দেশে মানুষ আধ্যাত্মিকতার অধিকতর অন্তস্থ ধরনের সন্ধান করছিল। কিন্তু খুব সামান্য সংখ্যকই যোগিদের মতো পূর্ণাঙ্গভাবে তা করতে পেরেছে। অ্যাক্সিয়াল যুগের অন্যতম দর্শন ছিল, পবিত্র ‘মহাশূন্যে’ অবস্থিত এমন কিছু নয়: এটা পৃথিবীতে প্রতিটি ব্যক্তির সত্তায় উপস্থিত এবং সর্বব্যাপী। ব্রাহ্মণ ও আত্মার পরিচয়ের উপনিষদের ভাষ্যে ধ্রুপদী ঢঙে প্রকাশিত একটি ধারণা। কিন্তু সত্তা আমাদের নিজস্ব সত্তার মতোই কাছাকাছি হলেও তা আবিষ্কার কঠিন বলেই প্রমাণিত হয়েছে। স্বর্গোদ্যানের দুয়ার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অতীতকালে পবিত্রতা মানুষের পক্ষে সুলভ চিন্তা করা হতো। প্রাচীন ধর্মগুলো বিশ্বাস করত, উপাস্য মানব-সন্তান এবং সকল প্রাকৃতিক ঘটনাবলী একই স্বর্গীয় উপাদানে গঠিত: মানুষ ও দেবতাদের মাঝে কোনও অস্তিত্বমূলক দূরত্ব ছিল না। কিন্তু অ্যাক্সিয়াল যুগের সূচনাকারী বিপর্যয়ের অংশ ছিল এই যে, পবিত্র বা স্বর্গীয় এই মাত্রাটি কোনওভাবে জগৎ হতে সরে গিয়ে এক অর্থে নারী-পুরুষের কাছে অচেনা হয়ে গিয়েছিল।
উদাহরণ স্বরূপ, হিব্রু বাইবেলের আদি টেক্সটে আমরা পড়ি যে, একজন সাধারণ পর্যটকের বেশে হাজির হওয়া ঈশ্বরের সঙ্গে আব্রাহাম একবার ভোজন পর্ব সেরেছিলেন।[১৬] মন্দিরে ঈশ্বরের দর্শন পাওয়ার পর মৃত্যু ভয়ে ভরে উঠেছিল ইসয়াহর মন।[১৭] জেরেমিয়াহ্ ঐশ্বরিকতাকে তাঁর হাত পা অবশ করে দেওয়া, হৃদয় মোচড়ানো ও মাতালের মতো বেসামাল করে দেওয়া যন্ত্রণা হিসাবে জানতেন।[১৮] সম্ভবত গৌতমের সমসাময়িক হয়ে থাকবেন ইযেকিয়েল, তাঁর গোটা জীবন একদিকে বর্তমানে পবিত্র এবং অন্যদিকে সচেতন, আত্ম- রক্ষাকারী সত্তার মাঝে বিরাজ করা মারাত্মক বিচ্যুতি তুলে ধরে। পয়গম্বরকে ঈশ্বর এমন উদ্বেগে আক্রান্ত করেছেন, তিনি কাঁপুনি থামাতে পারছেন নাঃ স্ত্রী মারা যাওয়ার পর ঈশ্বর তাঁকে শোক প্রকাশ করতে নিষেধ করেছেন: তাঁকে পশুর বিষ্ঠা খেতে বাধ্য করেছেন তিনি; বাধ্য করেছেন শরণার্থীর মতো ঠাসা ব্যাগ নিয়ে শহরময় ঘুরে বেড়াতে।[১৯] অনেক সময় স্বর্গীয় সত্তায় প্রবেশের জন্যে একজন সভ্য মানুষের স্বাভাবিক সাড়াকে অস্বীকার ও পার্থিব সত্তার বিরুদ্ধে সহিংস আচরণ প্রয়োজনীয় মনে হয়। আদি যোগিরাও তাদের অন্তরে বিরাজিত বলে বিশ্বাস করা অনিয়মিত ও চরম সত্তার উপলব্ধি করার লক্ষ্যে সাধারণ চৈতন্যে একই ধরনের আক্রমণের প্রয়াস পাচ্ছিল।
যোগিরা বিশ্বাস করত, কেবল তাদের স্বাভাবিক চিন্তন প্রক্রিয়া ধ্বংস, চিন্তা ও অনুভূতি নির্বাপিত করে আলোকনের বিরুদ্ধে যুদ্ধমান অবচেতন বাসনা মুছে ফেলতে পারলেই সত্তাকে মুক্ত করা যাবে। তারা প্রচলিত মানসিক অভ্যাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। অন্তস্থ আত্মার প্রতিটি পর্যায়ে যোগি স্বাভাবিকের উল্টো কাজ করত। সাধারণ সাড়াকে নাকচ করার জন্যেই নির্মাণ করা হয়েছিল প্রতিটি যোগ অনুশীল। যে কোনও ভাববাদীর মতো যোগি সমাজ হতে ‘বেরিয়ে গিয়ে’ আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু করত, কিন্তু তারপর আরেক ধাপ বেশি অগ্রসর হতো। কোনও গৃহস্থের মতো একই মানসিকতাও বহন করবে না সে: খোদ মনুষ্য সমাজ হতেই ‘বেরিয়ে যাচ্ছে’ সে। অশ্লীল জগতে পরিপূর্ণতার সন্ধান করার বদলে যাত্রার প্রতিটি পদক্ষেপে ভারতীয় যোগিরা এখানে বাস করতে অস্বীকৃতি জানাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল।
আলারা কালাম সম্ভবত ক্রমান্বয়ে গৌতমকে এই যোগ অনুশীলনগুলো দীক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু ধ্যান শুরু করার আগেই প্রথমে গৌতমকে নৈতিকতার শক্ত ভিত্তি স্থাপন করতে হয়েছিল যা তাঁকে মূল উপাদানে নামিয়ে এনে নৈতিক শৃঙ্খলা ও অহমবাদকে নিয়ন্ত্রণ করবে। যোগ অনুশীলনকারীকে এমন মনোসংযোগ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা দেয় যা স্বার্থপরতার লক্ষ্যে ব্যবহার করলে দানবীয় হয়ে উঠতে পারে। সুতরাং শিক্ষার্থীকে তাঁর অবাধ্য সত্তা (নিম্ন পর্যায়ের) শক্ত নিয়ন্ত্রণে আছে নিশ্চিত করার জন্যে চারটি ‘নিষেধাজ্ঞা’ (ইয়ামা) পালন করতে হতো। ইয়ামা শিক্ষার্থীর উপর চুরি, মিথ্যাচার, মাদক গ্রহণ, হত্যা বা অন্যান্য প্রাণীর ক্ষতি সাধন বা যৌনাচারে অংশ গ্রহণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করত। এইসব নিয়ম জৈনদের সাধারণ শিষ্যদের জন্যে নির্ধারিত নিয়মের অনুরূপ। বেশির ভাগ গাঙ্গেয় ভাববাদীদের ক্ষেত্রে যা সাধারণ বিষয় পরম মানসিক ও দৈহিক স্পষ্টতা অর্জনের জন্যে আকাঙ্ক্ষা প্রতিহত করার প্রতিজ্ঞা ও অহিংসার নীতির প্রতিফলন দেখায়। এইসব ইয়ামা দ্বিতীয় প্রকৃতিতে পরিণত না হলে গৌতমকে আরও অগ্রসর যোগ অনুশীলনের অনুমতি দেওয়া হতো না।[২০] নির্দিষ্ট কিছু নিয়মও (দৈহিক ও মানসিক অনুশীলন) অনুসরণ করতে হয়েছে তাঁকে, যার ভেতর বিবেকের পরিচ্ছন্নতা, ধম্ম পাঠ ও এক ধরনের স্বাভাবিক প্রশান্তি অর্জন অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেই সঙ্গে কৃচ্ছ্রতার অনুশীলনও (তপস) ছিল: শিক্ষাব্রতাঁকে বিনা অভিযোগে চরম শীত ও প্রচণ্ড গরমে, ক্ষুধা এবং পিপাসার মোকাবিলা করতে হতো। কথা ও ভাবভঙ্গিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হতো যাতে মনের ভাবনা কখনও প্রকাশিত হতে না পারে। সহজ প্রক্রিয়া ছিল না এটা। কিন্তু ইয়ামা ও নিয়ামায় দক্ষতা অর্জন করার পর গৌতম সম্ভবত ‘বর্ণনাতীত সুখ’ অনুভব করতে শুরু করেছিলেন যা কিনা ধ্রুপদী যোগ আমাদের জানাচ্ছে, এই আত্ম নিয়ন্ত্রণ, সংযম ও অহিংসার ফল।[২১]
এরপর গৌতম আসল যোগ অনুশীলনের প্রথমটি অনুসরণে প্রস্তুত হয়েছিলেন: আসন, যোগের বৈশিষ্ট্য শারীরিক ভঙ্গি।[২২] এই পদ্ধতির প্রতিটিতে মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা অস্বীকারের ব্যাপার রয়েছে। যোগির জগতকে অস্বীকার করার প্রথামিক নীতি তুলে ধরে। নড়াচড়া করতে অস্বীকৃতি জানানোর মাধ্যমে মন ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে শেখেন। পায়ের ওপর পা তুলে ঋজু ভঙ্গিতে নিশ্চল বসে থাকতে হতো তাঁকে। এতে তিনি হয়তো উপলব্ধি করে থাকবেন যে, স্বাধীন অবস্থায় আমাদের দেহ অবিরাম চলার ওপর থাকে: আমরা চোখ, পিঠ, কাঁধ চুলকাই, আড়মোড়া ভাঙ্গি, এক নিতম্ব হতে অন্য নিতম্বে ভর বদল করি, বিভিন্ন প্রণোদনায় সাড়া দিয়ে মাথা ঘোরাই। এমনকি ঘুমের ভেতরও আমরা আসলে স্থির থাকি না। কিন্তু আসনে যোগি এমন নিশ্চল থাকে যে তাকে মানুষের চেয়ে বরং কোনও মূর্তি বা গাছের মতো মনে হয়। অবশ্য একবার দক্ষতা অর্জন করার পর অস্বাভাবিক নিশ্চলতা অন্তস্থ প্রশান্তি প্রতিফলিত করে যা সে অর্জনের প্রয়াস পাচ্ছে।
এরপর শ্বাস-প্রশ্বাসে অস্বীকৃতি জানায় যোগি। শ্বাস-প্রশ্বাস সম্ভবত আমাদের শারীরিক কর্মকাণ্ডের সবচেয়ে মৌলিক, স্বয়ংক্রিয় এবং সহজাত অংশ, প্রাণ ধারণের জন্যে অনিবার্য। আমরা সাধারণত শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে ভাবি না। কিন্তু গৌতমকে এবার প্রাণায়ামের কৌশলে দক্ষতা অর্জন করতে হয়েছিল হয়তো-ক্রমাগত ধীর হতে ধীরে শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ।[২৩] চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল ক্রমাগত শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগের মাঝখানে যত দীর্ঘ সময় সম্ভব বিরতি দেওয়া যাতে শ্বাসপ্রশ্বাস একেবারে থেমে গেছে বলে মনে হয়। প্রাণায়াম নৈমিত্তিক জীবনের ছন্দোহীন শ্বাসপ্রশ্বাস হতে খুবই আলাদা। আমরা ঘুমের সময় যেভাবে শ্বাস- প্রশ্বাস ফেলি অনেকটা বরং সেই রকম, যখন স্বপ্ন ও সম্মোহিত অবস্থায় ইমেজারির সময়ে অবচেতন অনেক সুগম হয়ে ওঠে। শ্বাস-প্ৰশ্বাস গ্রহণে অস্বীকৃতি যোগির জগতকে অস্বীকার করাই দেখায় নাঃ শুরু থেকেই তার মানসিক অবস্থায় প্রাণায়ামের গভীর প্রভাব দেখা গেছে। প্রাথমিক অবস্থায় শিক্ষাব্রতী দেখত যে এটা এমন এক অনুভূতির জন্ম দেয় যা নিজের বাজানো বাজনার প্রভাবের সঙ্গে তুলনীয়: এক বিশালতার অনুভূতি পাওয়া যায়, বিশালত্ব ও শান্ত আভিজাত্য। যেন নিজের হাতে নিজ দেহের অধিকার নিচ্ছে কেউ।[২৪]
এইসব শারীরিক অনুশীলন আয়ত্ত করার পর একাগ্রতার পরবর্তী অনুশীলনের জন্যে প্রস্তুত হয়েছিলেন গৌতম। শিক্ষাব্রতী অন্য যে কোনও আবেগ বা সম্পর্ক বাদ দেওয়ার জন্যে কোনও ‘একটি বস্তু বা ধারণা’[২৫]র ওপর মনোসংযোগের শিক্ষা গ্রহণ করে, এবং মনে ভীড় জমানো বিচ্যুতির কোনওটাকেই স্থান দিতে অস্বীকৃতি জানায়।
ক্রমে নিজেকে স্বাভাবিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন গৌতম, চেষ্টা করছিলেন চিরন্তন সত্তার স্বাধীনতায় পৌঁছানোর। প্রত্যাহার (অনুভূতির প্রত্যাহার), যখন তাঁর অনুভূতিগুলো নিষ্ক্রিয় থাকে, কেবল বুদ্ধিমত্তা দিয়ে কোনও বস্তুকে চিন্তা করার ক্ষমতা, শিখেছেন তিনি।[২৬] ধরণায় (মনোসংযোগ) তাঁকে আপন সত্তার জমিনে প্রকৃত সত্তাকে ফুটিয়ে তোলা শেখানো হয়েছে, অনেকটা পকুরে ভাসমান পদ্মফুল বা অন্তস্থ আলোর মতো। ধ্যানের সময় শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ রেখে শিক্ষাব্রতী আপন সচেতনতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠার আশা করত, যেখানে মনে করা হয়েছে সে নিজের বুদ্ধিমত্তাকে ভেদ করে চিরন্তন আত্মার (পুরুসা) প্রতিফলন দেখতে পাবে।[২৭] প্রতিটি ধরণার মেয়াদ বারটি প্রাণায়াম- এর সমান হওয়ার কথা। বারটি ধরণা শেষে যোগি এমন গভীরভাবে নিজের মাঝে ডুবে যেত যে, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই একটা ‘ঘোর’ (ধ্যান: পালি ভাষায় ঝানা) অর্জন করত।[২৮]
টেক্সট জোর দিয়ে বলছে, এসবই আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমাদের চিন্তাভাবনার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটা মাদক প্রভাবিত অবস্থার মতোও নয়। কোনও দক্ষ যোগি এইসব অনুশীলনে নৈপূণ্য লাভ করার পর সাধারণত এক নতুন ধরনের প্রতিরক্ষা অর্জন করেছে বলে আবিষ্কার করত। অন্তত ধ্যানের সময়ের জন্যে হলেও। সে আর আবহাওয়ার ব্যাপারে উৎসাহী নয়। চৈতন্যের অস্থির ধারা নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে ও সত্তার মতোই পরিবেশের টেনশন ও পরিবর্তনের ব্যাপারে অভেদ্য হয়ে উঠেছে। এভাবে যে মানসিক ইমেজ বা বস্তুর ধ্যান করছিল তাতে বিলীন হয়ে গেছে বলে আবিষ্কার করত সে। কারণ সে স্মৃতিকে চাপা দিয়েছে, সাধারণত কোনও বস্তু যে বিশৃঙ্খল ব্যক্তিগত ইমেজ সৃষ্টি করে তার প্লাবনকে ঠেকিয়েছে; এখন আর নিজের গরজে এ থেকে বিচ্যুত নয় সে, একে সে বস্তুগতভাবে দেখছে না, বরং ‘যেমন ঠিক সেভাবেই’ দেখতে যাচ্ছে। যোগিদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ বাকধারা। তার চিন্তার জগৎ হতে ‘আমি’ মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে। এখন আর আপন অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে বস্তুকে দেখা হচ্ছে না। ফলে এমনকি একেবারে নিরস বস্তুও সম্পূর্ণ নতুন গুণাগুণ প্রকাশ করছে। কোনও কোনও শিক্ষাব্রতী এই পর্যায়ে প্রকৃতির পর্দা ভেদ করে পুরুসার ঝলক দেখার কথা কল্পনা করে থাকতে পারে।
এইসব কৌশল প্রয়োগ করে যোগি ধম্মের মতবাদের উপর ধ্যান করার সময় সেগুলো সম্পর্কে এমন স্পষ্ট অনুভূতি হয় যে এইসব সত্যের একটা যৌগিক গঠন তুলনায় ম্লান হয়ে যায়। আলারা কালাম একেই ‘প্রত্যক্ষ জ্ঞান’ বুঝিয়েছেন। যেহেতু স্বাভাবিক চেতনার বিভ্রম ও অহমবাদ আর যোগি ও ধম্মের মাঝখানে আসতে পারছে নাঃ বিকৃতকারী পর্দা বা বিষয়ানুগ সম্পর্কহীন নতুন স্পষ্টতার সঙ্গে ‘দেখছে’ সে একে। এইসব অভিজ্ঞতা বিভ্রম নয়। প্রাণায়াম অনুশীলনের ফলে সৃষ্ট মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনসমূহ যোগিকে তার মানসিক প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করার, এমনকি চেতনায় পরিবর্তন নিয়ে আসা অবচেতন প্রণোদনাগুলোকে পর্যবেক্ষণ করতে শিখিয়েছে। দক্ষ যোগি এখন সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব মানসিক কেরামতি দেখাতে পারবে। নির্দিষ্ট উপায়ে প্রশিক্ষিত হলে মন কীভাবে কাজ করে জানা হয়ে যায় তার। তখন দক্ষতার কল্যাণে নতুন নতুন গুণ আলোর দেখা পায়, ঠিক কোনও নৃত্য শিল্পী বা অ্যাথলেট যেভাবে মানবদেহের পূর্ণ দক্ষতার প্রদর্শন করে। আধুনিক গবেষকরা লক্ষ করেছেন, ধ্যানের সময় যোগির হৃৎপিণ্ডের গতি ধীর হয়ে আসে, মস্তিষ্কের ছন্দ ভিন্ন ধারায় বাঁক নেয়। স্নায়বিক দিক দিয়ে পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সে ও ধ্যানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে তীব্রভাবে স্পর্শকাতর হয়ে ওঠে।[২৯]
যোগি ভাবের ঘোরে (ঝানা) প্রবেশ করার পর ধারাবাহিকভাবে কিছু গভীর মানসিক অবস্থার ভেতর দিয়ে যায় সে, যার সঙ্গে সাধারণ অভিজ্ঞতার তেমন সম্পর্ক নেই। ঝানার প্রথম পর্যায়ে আশপাশের পরিবেশ সম্পর্কে একেবারে নির্বিকার হয়ে আনন্দ ও খুশির দারুণ অনুভূতি বোধ করে সে: যা কোনও যোগির পক্ষেই অর্জন করা সম্ভব। এটাই তার চূড়ান্ত মুক্তির সূচনা। তখনও বিক্ষিপ্ত চিন্তা থাকে তার, পলাতক ভাবনা খেলে যায় মনে। কিন্তু সে আবিষ্কার করেছে, এই ঘোরের সময় আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ ও যন্ত্রণার নাগালের বাইরে চলে গিয়েছিল সে। মুগ্ধ মনোসংযোগের সঙ্গে যার ধ্যান করছে সেই বস্তু, প্রতীক বা মতবাদের দিকে দৃষ্টিপাত করতে পারছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঝানায় যোগি এসব সত্যিকে এমনভাবে মিশে যায় যার ফলে তার চিন্তা পুরোপুর থেমে যায়। খানিক আগের নিখুঁত সুখের ব্যাপারেও আর সচেতনতা থাকে না। চতুর্থ ও চূড়ান্ত ঝানায় সে ধম্মের প্রতীক সমূহের সঙ্গে এমনভাবে মিশে যায় যেন ওগুলোর অংশ হয়ে গেছে সে। অন্য কিছু সম্পর্কে আর কোনও বোধ থাকে না। এইসব অবস্থার ভেতর অলৌকিক কোনও ব্যাপার নেই। যোগির জানা থাকে এসব সে নিজেই সৃষ্টি করেছে; তবে এখানে বিস্ময়ের কিছু নেই যে, আসলেই পৃথিবী ছেড়ে অভীষ্টের দিকে এগিয়ে যাবার কথা কল্পনা করেছে সে। সত্যিই নিপুণ হলে ঝানাকে অতিক্রম করে চারটি আয়তনের ধারায় প্রবেশ করতে পারে সে। এগুলো এতই প্রবল, আদি যোগিদের ধারণা ছিল যে তারা দেবতাদের বাসস্থানের এলাকায় প্রবেশ করেছে।[৩০] যোগি ক্রমাগতভাবে চারটি মানসিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করে যেগুলো তাকে সত্তার এক নতুন রূপের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে বলে মনে হয়: অসীমের বোধ, কেবল নিজ সম্পর্কে সচেতন এক খাঁটি চেতনাবোধ; বিপরীতভাবে পরিপূর্ণতায় ভরা অনুপস্থিতির একটা ধারণা। কেবল প্রতিভাবান যোগিরাই এই তৃতীয় আয়তনে পৌঁছতে পেরেছে। যাকে ‘কিছু না’ বলে, কারণ এর সঙ্গে জাগতিক অভিজ্ঞতার কোনও মিল নেই। এটা আরেকটা সত্তা নয়। একে বর্ণনা করার মতো পর্যাপ্ত শব্দ বা ধারণা নেই। সুতরাং একে ‘একটা কিছু’ বলার চেয়ে ‘কিছু না’ বলাই বেশি সঠিক। কেউ কেউ একে কোনও ঘরে প্রবেশ করে কিছু না পাওয়ার মতো বর্ণনা করেছেন: এক ধরনের শূন্যতা, স্থান ও মুক্তির অনুভূতি রয়েছে সেখানে।
একেশ্বরবাদীরা ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে একই ধরনের মন্তব্য করেছে। ইহুদি, ক্রিশ্চান ও মুসলিম ধর্মতাত্ত্বিকদের সবাই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মানবীয় চেতনায় সর্বোচ্চ স্বর্গীয় উৎসারণকে ‘কিছু না’ বলেছেন। তাঁরা এও বলেছেন যে ‘ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই’ বলাই ভালো, কারণ ঈশ্বর স্রেফ আরেকটা ঘটনা নন। দুর্ভেয় বা পবিত্রতার মুখোমুখি হলে ভাষা অসম্ভব সমস্যার মুখে হোঁচট খায় এবং এর ‘অন্যতা’র ওপর জোর দিতে অতিন্দ্রীয়বাদীরা সহজাতভাবে এই ধরনের ঋণাত্মক পরিভাষা বেছে নিয়েছে।[৩১] বোধগম্যভাবেই এইসব আয়তনে পৌঁছাতে সক্ষম যোগিরা অবশেষে তাদের সত্তার কেন্দ্ৰে বাসকারী অসীম সত্তার অভিজ্ঞতা লাভের কল্পনা করেছে। আলারা কালাম ‘কিছু না’র পর্যায়ে উন্নীত হওয়া তাঁর সময়ের অন্যতম যোগি ছিলেন। তাঁর দাবি, তিনি তাঁর অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য সত্তায় ‘প্রবেশ করেছেন’। গৌতম ছিলেন অবিশ্বাস্য প্রতিভাবান শিষ্য। সাধারণত যোগের জন্যে দীর্ঘ শিক্ষানবীশকালের প্রয়োজন হতো। জীবনব্যাপীও হতে পারত সেটা। কিন্তু খুবই অল্প সময়ে গৌতম তাঁর গুরুকে ‘কিছু না’র পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়ার কথা বলতে পেরেছিলেন। দারুণ খুশি হয়েছিলেন আলারা কালাম। সংঘের নেতৃত্ব দানে গৌতমকে অংশীদার হবার আমন্ত্রণ জানালেন তিনি। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করলেন গৌতম। আলারা কালামের গোত্রও ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি।
যোগ পদ্ধতি নিয়ে গৌতমের কোনও সমস্যা ছিল না। বাকী জীবন একে কাজে লাগাবেন তিনি। কিন্তু ধ্যানের অভিজ্ঞতার গুরুর দেওয়া ব্যাখ্যা তিনি মেনে নিতে পারেননি। এখানেই তিনি তাঁর সমগ্র ধর্মীয় জীবনকে বৈশিষ্ট্যায়িত করে তোলা অধিদবিদ্যিক মতবাদ সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কীভাবে ‘কিছু না’র পর্যায় অনিয়ন্ত্রিত ও অসৃষ্ট সত্তা হতে পারে যেখানে তিনি বেশ ভালো করেই জানেন যে এই অভিজ্ঞতা তাঁর নিজেরই সৃষ্টি? এই ‘কিছু না’ পরম হতে পারে না, কারণ তিনি নিজস্ব যোগ দক্ষতার সাহায্যে একে সৃষ্টি করেছেন। গৌতম ছিলেন নিষ্ঠুর রকম সৎ। তথ্য দিয়ে নিশ্চিত নয় এমন কোনও ব্যাখ্যায় নিজেকে প্রতারিত হতে দেবেন না তিনি। তাঁর অর্জিত চেতনার উন্নত অবস্থা নিব্বানা হতে পারে না, কারণ ঘোর হতে বেরিয়ে আসার পরও তীব্র আবেগ, আকাঙ্ক্ষা ও প্রলোভনের অধীনে রয়ে গেছেন তিনি, তাঁর অনঅনুপ্রাণিত লোভী সত্তাকেই বহন করে চলেছেন। অভিজ্ঞতার কারণে স্থায়ীভাবে বদলে যাননি। চিরস্থায়ী শান্তিও অর্জন করেননি। নিব্বানা অস্থায়ী হতে পারে না! নিব্বানা যেহেতু চিরন্তন, সুতরাং এটা শর্তের বিপরীত।[৩২] আমাদের সাধারণ জীবনের ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতি দুঃখের অন্যতম প্রধান কারণ, যন্ত্রণার অন্তহীন উৎস।
কিন্তু গৌতম যোগ অভিজ্ঞতার এই পাঠ নিয়ে শেষ চেষ্টা করতে প্রস্তুত ছিলেন। ‘কিছু না’র জমিন সর্বোচ্চ আয়তন নয়। ‘উপলব্ধি বা অনউপলব্ধি কোনওটাই নয়’, এমন একটি চতুর্থ মাত্রা রয়েছে। এমন হতে পারে, এই অতি পরিমার্জিত অবস্থা সত্তার দিকে অগ্রসর করে। তিনি জানতে পারেন উদ্দক রাজপুত্ত নামে এক যোগি এই সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর বিরল ভাগ্য লাভ করেছেন। উদ্দক তাঁকে এই সর্বোচ্চ অবস্থায় পৌঁছতে সাহায্য করতে পারবেন আশা করে তাঁর সংঘে যোগ দিতে যান। ফের সফল হন তিনি। কিন্তু আবার নিজের মাঝে ফিরে এসে গৌতম দেখতে পান তারপরেও আকাঙ্ক্ষা, ভয় ও ভোগান্তির শিকার রয়ে গেছেন তিনি। চূড়ান্ত যোগ জমিনে পৌঁছে তিনি সত্তার দেখা পেয়েছেন, উদ্দকের এই ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারেননি তিনি।[৩৩] এমনকি হতে পারে যে, এইসব অতিন্দ্রীয়বাদীরা যাকে চিরন্তন সত্তা বলেছেন, সেটা স্রেফ আরেকটা বিভ্রম? এইসব অনুশীলন যোগিকে কেবল ভোগান্তি হতে সাময়িক নিষ্কৃতিই দিতে পারে। সমক্ষ্য যোগ-এর অধিবিদ্যিক মতবাদ তাঁকে ব্যর্থ করেছিল, কারণ তা কোনও প্রতিভাবান যোগিকে চূড়ান্ত মুক্তি এনে দিতে পারেনি।
তো কিছু দিনের জন্যে যোগ ছেড়ে কৃচ্ছ্রতা (তপস) সাধনের দিকে মন দিলেন গৌতম। বনচারী সন্ন্যাসীদের কেউ কেউ সকল অশুভ কম্ম পুড়িয়ে দিয়ে তা মুক্তির দিকে নিয়ে যেতে পারে মনে করতেন। আরও পাঁচজন সাধকের সঙ্গে যোগ দিলেন তিনি। একসঙ্গে কঠোন সাধনা চালিয়ে গেলেন। যদিও মাঝে মাঝে নির্জনতার খোঁজ করেছেন গৌতম। এমনকি দিগন্তে কোনও রাখালের ছায়া চোখে পড়লেও বনে বাদারে পাগলের মতো ছুটে যেতেন। এই পর্যায়ে গৌতম হয় নগ্ন থাকতেন বা খুবই কর্কশ খড়ের আচ্ছাদন পরতেন। হাড় কাঁপানো শীতের রাতে খোলা জায়গায় ঘুমাতেন, কাঁটার বিছানায় শুতেন এবং এমনকি নিজের মলমূত্রও পান করতেন। এত দীর্ঘ সময় দম বন্ধ করে রাখতেন, মনে হতো বুঝি মাথা ফেটে যাবে। দুকানে ভীতিকর পর্দা সৃষ্টি হতো। খাওয়া বন্ধ করে দেওয়ায় ‘একসারি টাকুর মতো…কিংবা পুরোনো ছাপড়ার কড়িকাঠের মতো’ পাঁজরের হাড় বেরিয়ে পড়েছিল। পেটে হাত দিলেই বলতে গেলে মেরুদণ্ডের ছোঁয়া পেতেন। তাঁর চুল ঝরে পড়ে। গায়ের চামড়া কালো হয়ে কুঁচকে যায়। এক পর্যায়ে চলমান কয়েকজন দেবতা তাঁকে প্রাণের চিহ্নহীন অবস্থায় পথের পাশে পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁরা মনে করলেন মারা গেছেন তিনি। কিন্তু এসবই ব্যর্থ চেষ্টা, তাঁর কৃচ্ছ্রতা যত কঠোরই হোক, এমনকি হয়তো সেকারণেই তাঁর দেহ এখনও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছে। এখনও কামনা আর প্রলোভনে আক্রান্ত তিনি। আসলে যেন নিজের সম্পর্কে আগের চেয়ে ঢের বেশি সজাগ হয়ে উঠেছেন।[৩৪]
শেষ পর্যন্ত গৌতমকে মেনে নিতে নিতে হলো যে কৃচ্ছ্রতা সাধন যোগ সাধনার মতোই নিষ্ফল প্রমাণিত হয়েছে। নিজের অহমবাদের বিরুদ্ধে বীরত্বসূচক হামলা চালানোর পর যা অর্জন করেছেন সেটা হচ্ছে প্রকট হয়ে ওঠা পিঞ্জর এবং মারাত্মক দুর্বল শরীর। তিনি মারাই যেতে পারতেন হয়তো, কিন্তু নিব্বানার শান্তি অর্জন হতো না। এই সময় তিনি ও তাঁর পাঁচজন সঙ্গী প্রশস্ত নিরঞ্জরা নদীতীরে ঊরবেলার কাছাকাছি বাস করতেন। জানতেন অন্য পাঁচজন ভিক্ষু তাঁকে নেতা মেনে নিয়েছেন। তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন, তিনিই সবার আগে দুঃখ এবং পুনর্জন্মের চক্র হতে চূড়ান্ত মুক্তি অর্জন করবেন। কিন্তু তাঁদের হতাশ করেছেন তিনি। আপন মনে বলেছেন তিনি, তাঁর মতো অন্য কেউই নিজেকে এরচেয়ে কঠোর প্রায়শ্চিত্তের শিকার করতে পারবে না, কিন্তু নিজেকে মানবীয় সীমাবদ্ধতা হতে মুক্ত করার বদলে নিজের জন্যে কেবল আরও কষ্টেরই জন্ম দিয়েছেন তিনি। পথের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি। সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন, আলোকনের প্রচলিত উপায়গুলো অবলম্বন করেছেন। কিন্তু কোনওটাই কাজে আসেনি। সেই সময়ের মহান গুরুদের শিক্ষা দেওয়া ধৰ্ম্মগুলোকে মৌলিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ মনে হয়েছে। ওগুলোর বহু অনুশীলনকারীকেই তাঁর মতোই অসুস্থ, অসহায় ও জরাগ্রস্ত মনে হয়েছে।[৩৪] কেউ কেউ হয়তো হতাশ হয়ে অনুসন্ধানে ক্ষান্ত দিত, ফিরে যেত পেছনে ফেলে আসা আরামপ্রদ জীবন ধারায়। একজন গৃহস্থ হয়তো পুনর্জন্মের নিয়তির শিকার হতে পারে, কিন্তু সমাজ হতে ‘বেরিয়ে যাওয়া’ সাধকদেরও সেই একই পরিণতির শিকার মনে হয়েছে।
যোগি, সাধক ও বনচারী সন্ন্যাসীদের সবাই বুঝতে পেরেছিলেন যে, আত্মসচেতনতা ও চিরন্তনভাবে লোভী অহমই সমস্যার মূল। নারী ও পুরুষকে অবিরাম নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত মনে হয়। এটা তাদের পক্ষে পবিত্র শান্তির বলয়ে প্রবেশ অসম্ভব করে তুলেছে। নানা উপায়ে এই অহমবাদকে বিনাশ করে সচেতন অবস্থার অস্থির স্রোতের আর অচেতন বাসনার অতীতে পরম এক নীতির কাছে যাবার প্রয়াস পেয়েছে তারা। মনের গভীরে তার দেখা পাবে বলে বিশ্বাস ছিল তাদের। যোগি ও সাধকরা বিশেষ করে এই জাগতিক বিশ্ব হতে পালাতে চেয়েছিলেন যাতে বাহ্যিক অবস্থার ব্যাপারে নিরাসক্ত হয়ে উঠতে পারেন। অনেক সময় তাদের কোনওমতে বেঁচে আছেন বলে মনে হতো। অহমবাদ কতটা বিপজ্জনক হতে পারে, তারা জানতেন। অহিংসার আদর্শ দিয়ে সেটা দূর করার প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু এই স্বার্থপরতাকে চাপা দেওয়া প্রায় অসম্ভব মনে হয়েছে। এইসব কৌশলের কোনওটাই গৌতমের কাজে আসেনি। তাঁর সেক্যুলার সত্তাকে অপরিবর্তিত রেখে দিয়েছে ওগুলো। এখনও তিনি আকাঙ্ক্ষায় আক্রান্ত। এখনও চেতনার ফাঁদে আটকা পড়ে আছেন। পবিত্র সত্তা কোনওরকম কুহক কিনা সন্দেহ জেগেছিল তাঁর মনে, সম্ভবত ভাবতে শুরু করেছিলেন যে, এটা তাঁর কাঙ্ক্ষিত চিরন্তন, নিয়ন্ত্রিত বাস্তবতার সহায়ক প্রতীক নয়। কোনও উন্নত সত্তার অনুসন্ধান হয়তো অহমবাদকে সমর্থন করতে পারে যাকে বিনাশ করা প্রয়োজন। যা হোক, আশা হারাননি গৌতম। তিনি নিশ্চিত ছিলেন, মানুষের পক্ষে আলোকনের চূড়ান্ত মুক্তিতে পৌঁছানো সম্ভব। এখন থেকে তিনি কেবল আপন অন্তর্দৃষ্টির উপর নির্ভর করবেন। তাঁর বেলায় আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠিত ধরণ ব্যর্থ হয়েছে। তাই নিজস্ব ধরণ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। অন্য কোনও গুরুর ধম্ম মানবেন না বলে স্থির করলেন। ‘নিশ্চয়ই,’ চিৎকার করে বললেন তিনি, ‘আলোক প্রাপ্তির নিশ্চয়ই আরও পথ আছে!’[৩৬]
ঠিক সেই মুহূর্তে, যখন তিনি রুদ্ধ পথে এসে পৌঁছেছেন বলে মনে হয়েছে, নতুন এক সমাধান আপনাআপনি হাজির হয়েছিল তাঁর সামনে।
তথ্যসূত্র
১. সুত্তা-নিপাতা ৩: ১।
২. ট্রেভর লিঙ, দ্য বুদ্ধা: বুড্ডিস্ট সিভিলাইজেশন ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড সিলোন, লন্ডন, ১৯৭৩, ৭৬-৮২; হারমান অলদেনবার্গ, দ্য বুদ্ধা: হিজ লাইফ, হিজ ডকট্রিন, হিজ অর্ডার (অনু. উইলিয়াম হোয়ে), লন্ডন, ১৮৮২, ৬৬-৭১; মাইকেল কারিথার্স, দ্য বুদ্ধা, অক্সফোর্ড ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৩, ১৮-২৩; সুকুমার দত্ত, বুড্ডিস্ট মঙ্কস অ্যান্ড মনেস্টারিজ ইন ইন্ডিয়া, লন্ডন, ১৯৬২, ৩৮-৫০।
৩. লিঙ, দ্য বুদ্ধা, ৭৭-৭৮।
৪. রিচার্ড এফ. গোমব্রিচ, থেরাভেদা বুদ্ধজম: আ সোশ্যাল হিস্ট্রি ফ্রম অ্যানশেন্ট বেনারেস টু মডার্ন কলোম্বো, লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৮, ৪৭।
৫. প্রাগুক্ত, ৪৮-৪৯।
৬. অলদেনবার্গ, দ্য বুদ্ধা, ৬৭।
৭. কারিথার্স, দ্য বুদ্ধা, ২৫।
৮. লিঙ, দ্য বুদ্ধা, ৭৮-৮২; জোসেফ ক্যাম্পবেল, অরিয়েন্টাল মিথোলজি : দ্য মাস্কস অভ গড, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬২, ২১৮-৩৪।
৯. লিঙ, দ্য বুদ্ধা, ৯২; মির্চা এলিয়াদ, ইয়োগা, ইমমর্টালিটি অ্যান্ড ফ্রিডম (অনু. উইলিয়াম জে. ট্রাস্ক), লন্ডন, ১৯৫৮, ১০২।
১০. সমক্ষ্য কারিতা ৫৯।
১১. এলিয়াদ, ইয়োগা, ৮-৩৫।
১২. মাজহিমা নিকয়া, ২৬, ৩৬, ৮৫, ১০০।
১৩. ধ্রুপদী যোগের আলোচনার জন্যে এলিয়াদ, ইয়োগা, ৩৫-১১৪।
১৪. প্রাগুক্ত, ৪-৫।
১৫. গ্যালাশিয় ৪: ১-১১।
১৬. জেনেসিস ১৮cf. দ্য অ্যাক্টস অভ দ্য অ্যাপসলস্ ১৪: ১১-১৭, যেখানে লিস্ট্রার জনগণ মনে করেছিল, পল এবং বারনাবাস দেবতা জিউস ও হার্মেসের অলৌকিক প্ৰকাশ।
১৭. ইসায়াহ্ ৬: ৫।
১৮. জেরেমিয়াহ্ ৪৪: ১৫-১৯।
১৯. ইযেকিয়েল ৪: ৪-১৭; ১২: ২৪: ১৫-২৪।
২০. এলিয়াদ, ইয়োগা, ৫৯-৬২।
২১. ইয়োগা-সুত্তা ২: ৪২।
২২. এলিয়াদ, ইয়োগা, ৫৩-৫৫।
২৩. প্রাগুক্ত, ৫৫-৫৮।
২৪. প্রাগুক্ত, ৫৬।
২৫. প্রাগুক্ত, ৪৭-৪৯।
২৬. প্রাগুক্ত, ৬৮-৬৯।
২৭. প্রাগুক্ত, ৭০-৭১।
২৮. প্রাগুক্ত, ৭২-৭৬: ১৬৭-৭৩: কারিথার্স, দ্য বুদ্ধা, ৩২-৩৩; এডোয়ার্ড কনযে, বুড্ডিস্ট মেডিটেশন, লন্ডন, ১৯৫৬, ২০-২২।
২৯. করিথার্স, দ্য বুদ্ধা, ৩০, ৩৪-৩৫।
৩০. প্রাগুক্ত, ৩৩; এলিয়াদ, ইয়োগা, ৭৭-৮৪।
৩১. ক্যারেন আর্মস্ট্রং, আ হিস্ট্রি অভ গড, লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৯৩। [বর্তমান অনুবাদকের অনুবাদে স্রষ্টার ইতিবৃত্ত নামে একুশে বইমেলায় (২০১০) রোদেলা প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত]
৩২. মাজহিমা নিকয়া, ২৬,৩৬, ৮৫, ১০০।
৩৩. প্রাগুক্ত।
৩৪. প্রাগুক্ত, ১২, ৩৬, ৮৫, ২০০
৩৫. প্রাগুক্ত, ৩৬।
৩৬. প্রাগুক্ত।
৩. আলোকন
কিংবদন্তী ইংগিত দেয় যে, গৌতমের ছেলেবেলা আমাদের আধ্যাত্মিক পরিপক্বতা এনে দেওয়ার মতো একমাত্র জ্ঞান দুঃখ-কষ্টের ধারণা হতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় অজাগ্রত পর্যায়ে কেটে গেছে। কিন্তু পরবর্তী বছরগুলোয় তিনি স্মৃতিচারণ করেছেন যে, এমন একটা মুহূর্ত গেছে যখন সত্তার অন্য ধরনের একটা আভাস দেওয়া হয়েছিল তাঁকে। বাবা পরবর্তী বছরের শস্যের বীজ বপনের আগে ক্ষেতে লাঙল-উৎসব দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে। গ্রাম ও শহরের সমস্ত পুরুষ অংশ নিয়েছিল বাৎসরিক এই অনুষ্ঠানে। তো শুদ্ধোদন তাঁর শিশু ছেলেকে পরিচারিকাদের হাতে হাওলা করে একটা গোলাপজাম গাছের ছায়ায় রেখে কাজে গেলেন। কিন্তু পরিচারিকারা লাঙল দেওয়া দেখবে বলে চলে গেল সেখান থেকে। নিজেকে একাকী আবিষ্কার করে উঠে বসলেন গৌতম। এই কাহিনীর একটি ভাষ্যে আমাদের বলা হয়েছে, তিনি যে ক্ষেতে লাঙল দেওয়া হচ্ছিল সেটার দিকে তাকিয়েছিলেন। এমন সময় লক্ষ করলেন, কচি ঘাসগুলো উপড়ে গিয়েছে। এইসব নতুন গজানো চারায় পোকামাকড়ের পারা ডিমগুলোও নষ্ট হয়ে গেছে। ধ্বংসযজ্ঞের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত এক বেদনা বোধ করেছিলেন ছোট সেই মানুষটি, যেন তাঁর অতি নিকটাত্মীয়দের হত্যা করা হয়েছে।[১] কিন্তু দিনটা ছিল চমৎকার, তাঁর মনের ভেতর নিখাঁদ আনন্দের অনিরুদ্ধ অনুভূতি জেগে উঠল। আমাদের সবারই এমন মুহূর্তের অভিজ্ঞতা আছে। অপ্রত্যাশিত ও আমাদের দিক থেকে কোনওরকম জোরাল প্রয়াস ছাড়াই আসে সেটা। আসলে যখনই আমরা আমাদের সুখ নিয়ে ভাবতে যাই, জানতে চাই কেন আমরা খুশিতে ভরে উঠেছি, তখনই আত্মসচেতন হয়ে ওঠায় সেই অনুভূতি মিলিয়ে যায়। নিজের সত্তাকে এর মাঝে টেনে আনলে এই অপূর্বচিন্তিত আনন্দ বজায় থাকতে পারে নাঃ এটা আবশ্যিকভাবেই পরমানন্দের একটা মুহূর্ত, এক তুরীয় আনন্দ যা আমাদের দেহ আর আমাদের নিজস্ব অহমবাদের প্রিজমের বাইরে নিয়ে যায়। এ জাতীয় extasis: এমন এক শব্দ যার আক্ষরিক অর্থ ‘সত্তার বাহরে অবস্থান করা,’: এর সঙ্গে আমাদের যাপিত জীবনের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণকারী আকাঙ্ক্ষা ও লালসার কোনও সম্পর্ক নেই। পরবর্তীকালে গৌতম যেমন স্মৃতিচারণ করেছেন, ‘এর অবস্থান তানহাকে জাগিয়ে তোলা বস্তু হতে দূরে।’ ছোট ছেলেটি যখন ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে সম্পর্কহীন প্রাণীদের যন্ত্রণাকে নিজের হৃদয়ে প্রবেশ করতে দিয়েছেন, তখন স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতির একটা মুহূর্ত তাঁকে নিজের মধ্যে হতে বের করে দিয়েছে। স্বার্থহীন করুণার জোয়ার মুহূর্তের আত্মিক মুক্তি এনে দিয়েছিল তাঁকে।
সহজাত প্রবৃত্তির বশেই ছেলেটি পায়ের উপর পা তুলে আসনে বসার ভঙ্গিতে ঋজু ঢঙে বসেছিলেন। জন্ম যোগি হিসাবে প্রথম ঝানায় প্রবেশ করেছিলেন তিনি। এমন এক মোহাবস্থা যেখানে ধ্যানী শান্ত সুখ বোধ করেন, আবার চিন্তা ভাবনাও করতে পারেন।[২] কেউ তাঁকে যোগের কৌশল শেখাননি, কিন্তু কয়েক মুহূর্তের জন্যে তিনি এমন এক স্বাদ আস্বাদন করেছিলেন যা নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়ার মতো। ধারাভাষ্য আমাদের জানাচ্ছে, প্রাকৃতিক জগৎ তরুণ গৌতমের আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা শনাক্ত করেছিল। দিন গড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য গাছের ছায়া সরে গেলেও গোলাপজাম গাছের ছায়া অনড় থেকে তীব্র সূর্যের হাত থেকে ছায়া দিয়ে যাচ্ছিল তাঁকে। পরিচারিকারা ফেরার পর এই অলীক ঘটনা দেখে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। শুদ্ধোদনকে ডেকে আনে তারা। ছোট ছেলেকে শ্রদ্ধা জানান তিনি। শেষ এই উপাদানটি নিশ্চিতভাবে কল্পিত, কিন্তু মোহাবেশের কাহিনী, ঐতিহাসিক হোক বা না হোক, পালি কিংবদন্তীতে গুরুত্বপূর্ণ; কথিত আছে, গৌতমের আলোকপ্রাপ্তিতে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।
আশা-নিরাশা মেশানো কণ্ঠে ‘নিশ্চয়ই আলোকনের আরও উপায় আছে,’ বলে চেঁচিয়ে ওঠার অনেক বছর পর গৌতম ছোটবেলার এই অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ করেছেন। ঠিক এই মুহূর্তে-আবার অপূর্বচিন্তিত ও অপ্রত্যাশিত- ছোটবেলার সেই পরমানন্দের স্মৃতি মনের উপরিতলে উঠে এসেছে তাঁর। শীর্ণকায়, পরিশ্রান্ত ও মারাত্মক অসুস্থ গৌতম ‘গোলাপজাম গাছের শীতল ছায়ার’ কথা মনে করেছেন, যা অনিবার্যভাবে মনের মাঝে নিব্বানার ‘শীতলতা’ নিয়ে এসেছিল। বেশির ভাগ যোগি বহু বছরের কঠোর পরিশ্রমের পর কেবল প্রথম ঝানা অর্জন করতে পারে। কিন্তু তাঁর দিক থেকে কোনও প্রয়াস ছাড়াই উপস্থিত হয়েছে এটা, তাঁকে নিব্বানার আভাস দিয়েছে। কাপিলাবাস্তু ছাড়ার পর থেকেই আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে সংগ্রামের অংশ হিসাবে সকল সুখ বিসর্জন দিয়েছিলেন তিনি। কৃচ্ছ্রতা সাধনের বছরগুলোয় আপন দেহ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন প্রায়। আশা ছিল, এভাবে নিজেকে মানুষের স্বাভাবিক দুর্দশাগ্রস্ত অস্তিত্বের বিপরীত পবিত্র জগতে ঠেলে দিতে পারবেন। অথচ ছোটবেলায় এক নিখাদ আনন্দের অভিজ্ঞতার পর বিনা ঝামেলাতেই যোগের পরমান্দ লাভ করেছিলেন তিনি। গোলাপজাম গাছের শীতলতার কথা ভাববার সময় দুর্বল অবস্থায় সুদীর্ঘ জ্বরে ভোগার পর খিঁচুনি হতে মুক্তি পাওয়ার কথা কল্পনা করেছেন তিনি। এরপর এক অনন্যসাধারণ ধারণা আঘাত করেছে তাঁকে। ‘এটাই কি’, নিজেকে জিজ্ঞেস করেছেন তিনি, ‘আলোকনের উপায়?’ অন্য গুরুরা কি ভুল করেছেন? আমাদের অনিচ্ছুক সত্তাকে চূড়ান্ত মুক্তি অর্জনের জন্যে নিপীড়ন করার বদলে আমরা হয়তো অনায়াসে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবেই তা অর্জন করতে পারি। নিব্বানা কি আমাদের মানবীয় কাঠামোরই অন্তস্থ নির্মাণ? একজন অপ্রশিক্ষিত বালক প্রথম ঝানায় পৌঁছতে পারলে আর বিনা চেষ্টায় নিব্বানার আভাস লাভ করতে পারলে যোগ-দর্শন নিশ্চয়ই মানুষের পক্ষে গভীরভাবে স্বাভাবিক। যোগকে মানুষের উপর হামলা বানানোর বদলে একে কি সেতো-বিমুক্তি, অর্থাৎ ‘মনের উন্মুক্তি’ আনয়নকারী অন্তস্থ প্রবণতা গড়ে তোলার কাজে ব্যবহার করা যায়, যা কিনা পরম আলোকনের প্রতিশব্দ?
ছেলেবেলার অভিজ্ঞতা নিয়ে চিন্তাভাবনা করার পরপরই গৌতম নিশ্চিত হয়ে যান, তাঁর ধারণা সঠিক। এটাই নিব্বানার প্রকৃত পথ। এখন কেবল প্রমাণ করার পালা। কেন এত সহজে প্রথম ঝানায় পৌঁছে দেওয়া প্রশান্ত সুখের আবেশ সৃষ্টি হয়েছিল? একটা অত্যাবশ্যকীয় উপাদান ছিল গৌতমের ভাষায়, “বিচ্ছিন্নতা’। তাঁকে একা রেখে যাওয়া হয়েছিল : পরিচারিকারা গল্পগুজবে তাঁর মন বিক্ষিপ্ত করে রাখলে কখনওই তিনি পরমান্দের পর্যায়ে যেতে পারতেন না। ধ্যানের জন্যে একান্ত পরিবেশ ও নৈঃশব্দ্য প্রয়োজন। কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতা শারীরিক নিঃসঙ্গতার অতিরিক্ত। গোলাপজাম গাছের নিচে বসে থাকবার সময় তাঁর মন বস্তুগত জিনিস এবং অপূর্ণাঙ্গ ও অলাভজনক যেকোনও কিছু হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। গৌতম ছয় বছর আগেই বাড়ি ছেড়েছিলেন বলে আপন মানবীয় প্রকৃতিকে আলোকিত করে প্রতিটি প্রবণতা ধ্বংস করে দিচ্ছিলেন। যেকোনও রকম সুখকে অবিশ্বাস করতে শিখেছিলেন তিনি। কিন্তু এবার নিজেকে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, বহু আগের অপরাহ্নের সেই সুখানুভূতিকে কেন ভয় পাবেন? সেই নিখাদ আনন্দের সঙ্গে লোভী বাসনা বা ইন্দ্রিয়জ আকাঙ্ক্ষার কোনওই সম্পর্ক ছিল না। কিছু কিছু সুখানুভূতি সত্যি সত্যি অহমবাদ হতে মুক্ত করে উন্নত যোগ অবস্থায় পৌঁছে দিতে পারে। নিজেকে আবার প্রশ্নটা করামাত্র নিজস্ব আত্মবিশ্বাসী চূড়ান্ত সুরে সাড়া দিলেন গৌতম: ‘আমি অমন আনন্দে ভীত নই,’ বললেন তিনি।[৩] সেই ঘোরের দিকে এগিয়ে যাবার নিঃসঙ্গতা সৃষ্টি করাই আসল কথা এবং মনের সেই সামগ্রিক (কুসলা) অবস্থাকে লালন করা যা নিরাসক্ত দরদে কীটপতঙ্গ ও ঘাসের চারার জন্যে দুঃখবোধ করতে প্রাণিত করছিল তাঁকে। একই সাথে আলোকপ্রাপ্তিতে কাজে আসবে না বা বাধা সৃষ্টি করবে, এমন মানসিক অবস্থা সতর্কতার সঙ্গে পরিহার করে যাবেন।
অবশ্য ‘পাঁচ নিষেধাজ্ঞা’ পালনের ভেতর দিয়ে আগে থেকেই এই আলোকেই চলছিলেন তিনি, যা সহিংসতা, মিথ্যাচার, চুরি, মাদকাসক্তি ও যৌনতার মতো ‘অনুপযোগি’ (অকুসলা) কর্মকাণ্ড নাকচ করেছে। কিন্তু এবার তিনি বুঝতে পারলেন, এটাই যথেষ্ট নয়। অবশ্যই তাঁকে এই পাঁচটি বাধার বিপরীত ইতিবাচক প্রবণতা গড়ে তুলতে হবে। পরবর্তীকালে তিনি বলবেন, আলোকন প্রত্যাশী কোনও ব্যক্তিকে অবশ্যই এইসব ‘সহযোগি’ ‘সামগ্রিক’ বা ‘দক্ষ’ (কুসলা) অবস্থার সন্ধানে ‘শক্তিমান, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও অধ্যাবসায়ী’ হতে হবে যা আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের বিকাশ ঘটাবে। অহিংসা কেবল সামান্য দূর এগিয়ে দিতে পারবে; সহিংসতা বর্জনের বদলে শিক্ষাব্রতাঁকে অবশ্যই সবকিছু ও সবার সঙ্গে কোমল ও দয়াময় আচরণ করতে হবে; তাকে অবশ্যই অশুভ ইচ্ছার ক্ষীণ অনুভূতি ঠেকাতে প্রেম-প্রীতির অনুভূতি গড়ে তুলতে হবে। মিথ্যা না বলাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু ‘সঠিক কথা’ বলা ও আপনি যা বলছেন ‘সেটা যৌক্তিক, সঠিক, পরিষ্কার এবং উপকারী’ হওয়াটা নিশ্চিত করতে হবে। চুরি হতে নিবৃত্ত থাকা ছাড়াও একজন ভিক্ষু যা দেওয়া হচ্ছে তাতেই ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ প্রকাশ না করেই ইতিবাচকভাবে আনন্দ প্রকাশ করতে হবে, তাঁকে সবসময়ই খুশি থাকতে হবে।[৪] যোগিরা সবসময় বলেছে, পাঁচটি নিষেধাজ্ঞার অনুসরণ ‘অসীম সুখ’ বয়ে আনবে, কিন্তু মনের এই ইতিবাচক অবস্থার সৃষ্টি সচেতন প্রয়াসে এই ধরনের exstasis নিঃসন্দেহে দ্বিগুণ হবে। গৌতম বিশ্বাস করতেন, এই ‘দক্ষতাপূর্ণ’ আচরণ দ্বিতীয় স্বভাবের মতো অভ্যাসে এসে গেলে শিক্ষাব্রতী ‘নিজের মাঝে নিখাঁদ আনন্দ অনুভব’ করবে, ছেলেবেলায় গোলাপজাম গাছের নিচে যে আনন্দ বোধ করেছিলেন তিনি সেটার অনুরূপ না হলেও সমরূপ।[৫]
টেক্সট অনুযায়ী প্রায় প্রুস্তিয় এই স্মৃতিচারণ গৌতমের জন্যে বাঁক বদলকারী ঘটনা ছিল। সেই থেকে মানুষের স্বাভাবের বিপক্ষে যুদ্ধ করার বদলে তার সঙ্গে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন-আলোকনের পক্ষে অনুকূল মানসিক অবস্থাকে বাড়িয়ে তুলে তার সম্ভাবনাকে বাধাগস্ত করার মতো যেকোনও কিছুকে এড়িয়ে যাওয়া। গৌতম তাঁর ভাষায়, ‘মধ্যপন্থা’ গড়ে তুলছিলেন যা একদিকে যেমন শারীরিক ও আবেগগত আত্মপ্রশ্রয় বর্জন করেছে, অন্যদিকে বাদ দিয়েছে চরম কৃচ্ছ্রতা সাধনও যা সমান মাত্রায় বিধ্বংসী হতে পারে। তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, পাঁচ সঙ্গীর সঙ্গে অনুসরণ করা শাস্তিমূলক পদ্ধতি অবশ্যই ত্যাগ করতে হবে যা তাঁকে এমন অসুস্থ করে দিয়েছে যে মুক্তির প্রাকশর্ত ‘খাঁটি আনন্দ’ বোধ করার কোনও উপায়ই নেই এখন। টেক্সট অনুযায়ী কয়েক মাসের ভেতর প্রথমবারের মতো কুম্মাসা নামে দুধের পায়েস বা ফিরনি দিয়ে শক্ত খাবার গ্রহণ করলেন তিনি। তাঁকে খেতে দেখে ভিক্ষুরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। বিতৃষ্ণার সঙ্গে সরে গিয়েছেন তাঁরা। গৌতম আলোকনের জন্যে সংগ্রাম ত্যাগ করছেন, এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিলেন।[৬]
কিন্তু অবশ্যই মোটেই তেমন কিছু ছিল না ব্যাপারটা। গৌতম নিশ্চয়ই আপন পরিচর্যায় স্বাস্থ্য উদ্ধার করেছিলেন। এই সময়ে সম্ভবত নিজস্ব ধরনের যোগ সাধনা গড়ে তুলতে শুরু করেন তিনি। তিনি আপন চিরন্তন সত্তার দেখা পাওয়ার আশা করছিলেন না, কেননা তখন ভাবতে শুরু করেছিলেন যে, এটা মানুষকে আলোকন হতে দূরে সরিয়ে রাখা আরেকটা বিভ্রম মাত্র। মানবীয় প্রকৃতির সঙ্গে আরও একাত্ম হতে সাহায্য করার লক্ষ্যেই তাঁর যোগ নির্মিত হয়েছিল যাতে নিব্বানা অর্জনের পথে একে কাজে লাগাতে পারেন তিনি। প্রথমে ধ্যানের প্রস্তুতি হিসাবে এসেছে ‘অভিনিবেশ’ (সাতি) নামের অনুশীলন, যেখানে দিনের প্রতিটি মুহূর্তে নিজ আচরণ নিরীক্ষা করেছেন তিনি। সচেতনতার ওঠা-নামার সাথে সাথে নিজের অনুভূতি ও চাঞ্চল্যের জোয়ার ভাটা জরিপ করেছেন। ইন্দ্রিয়জ বাসনা দেখা দিলেই সেটাকে স্রেফ দমন না করে তার আবির্ভাবের কারণ এবং কতটা দ্রুত মিলিয়ে গেছে, লক্ষ করতেন তিনি। বাহ্যিক জগতের সঙ্গে বোধ ও চিন্তার মিথষ্ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেছেন। প্রতিটি দৈহিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সজাগ করে তুলেছেন নিজেকে। কীভাবে হাঁটছেন, উবু হওয়া কি হাত-পা মেলে রাখা, এবং ‘খাওয়া, পান করা, চিবানো, স্বাদ গ্রহণ, বর্জত্যাগ, হাঁটা, দাঁড়ানো, বসা, ঘুমানো, জেগে ওঠা, কথা বলা ও নীরব থাকা’র[৭] সময় নিজের আচরণ সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠেন। বিভিন্ন ধরনের ধারণা কীভাবে মনের ভেতর খেলে যায়, সংক্ষিপ্ত আধঘণ্টা সময়ে আকাঙ্ক্ষা ও বিরক্তির অবিরাম ধারা আক্রান্ত করতে পারে তাঁকে, যেসব লক্ষ্য করেছেন। আকস্মিক কোনও শব্দ বা তাপমাত্রায় পরিবর্তনে তিনি কেমন করে সাড়া দিচ্ছেন সেদিকে “মনোযোগী” হয়ে ওঠেন তিনি। দেখেছেন কত দ্রুত অতি তুচ্ছ জিনিসও তাঁর মনের শান্তি নষ্ট করছে। এই ‘অভিনিবেশ’ স্নায়বিক অন্তর্মুখীতার চেতনায় বিকশিত হয়নি। গৌতম ‘পাপে’র প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে নিজ মনুষ্যত্বকে এভাবে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে স্থাপন করেননি। তাঁর ব্যবস্থায় পাপের কোনও স্থান নেই, কেননা যেকোনও অপধারই স্রেফ ‘অনুপযোগি’ হয়ে দাঁড়াবে: এটা শিক্ষাব্রতীর ভেতর সেই অহমই রোপন করবে সে যা অতিক্রম করার প্রয়াস পাচ্ছে। গৌতমের ব্যবহৃত কুসলা ও অকুসলা শব্দ দুটি তাৎপর্যপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ, পাপপূর্ণ হওয়ার কারণে নয় বরং বরং নিব্বানা অর্জনে ব্যক্তিকে সাহায্য করবে না বলেই যৌনতা পাঁচটি ইয়ামার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। যৌনতা মানুষকে সামসারায় বন্দিকারী আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এতে যে শক্তি ব্যয় হয় তা যোগে নিয়োজিত করাই শ্রেয়। কোনও ক্রীড়াবিদ যেমন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতার আগে নির্দিষ্ট খাবার গ্রহণে বিরত থাকে একজন ভিক্ষুও তেমনি যৌনতা হতে বিরত থাকেন। যৌনতার প্রয়োজন আছে, কিন্তু ‘মহান অনুসন্ধানে’ নিয়োজিত কারও পক্ষে তা ‘উপযোগি’ নয়। অনুভূতির ওপর হামলে পড়বেন বলে নিজ মানবীয় প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করছিলেন না গৌতম, বরং এর ক্ষমতা কাজে লাগাতে এর কার্যধারা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে উঠছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তাঁর নিজের মাঝেই দুঃখ-কষ্টের সমাধান নিহিত রয়েছে, যাকে তিনি বলেছেন, ‘এই ফ্যাদম-দীর্ঘ শরীরে, এই দেহমনে।’[৮] নিজ জাগতিক স্বভাবের পরিমার্জনের মধ্য দিয়েই আসবে মুক্তি। সুতরাং তাঁকে এর তদন্ত করতে হবে এবং এমন নিবিড়ভাবে জানতে হবে যেমন করে তালিম দেওয়ার সময় সওয়ারি ঘোড়াকে চিনে নেয়।
কিন্তু অভিনিবেশের অনুশীলন তাঁকে আগের চেয়ে আরও প্রকটভাবে দুঃখ- কষ্ট ও তার উৎস আকাঙ্ক্ষার সর্বব্যাপীতা সম্পর্কে সজাগ করে তুলেছিল। তাঁর সচেতনতায় ভিড় জমানো এইসব চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল খুবই ক্ষণস্থায়ী। সমস্ত কিছুই অস্থায়ী (অনিক্য)। বাসনা যত প্রখরই হোক না কেন, অচিরেই ক্ষয়ে যায় ও সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু তার জায়গা দখল করে। কিছুই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এমনকি ধ্যানের সুখও নয়। জীবনের ক্ষণস্থায়ী রূপই ভোগান্তির অন্যতম প্রধান কারণ। প্রতি মুহূর্তের অনুভূতি লক্ষ করতে গিয়ে গৌতম আরও সচেতন হয়ে উঠলেন যে, জীবনের দুঃখ অসুস্থতা, বয়স ও মৃত্যুতে সীমাবদ্ধ নয়। এটা দৈনিক, এমনকি ঘণ্টা হারেও ঘটে। ছোট ছোট হতাশা, প্রত্যাখ্যান, নিরাশা ও ব্যর্থতার ভেতর দিয়ে কোনও এক দিনে আমাদের ওপর আপতিত হয়: ‘যন্ত্রণা, শোক ও হতাশাই দুঃখ,’ পরবর্তী সময়ে ব্যাখ্যা করবেন তিনি, ‘আমরা যার কাছাকাছি হতে বাধ্য হওয়া ঘৃণা করি সেটাই ভেগান্তি, আমরা যা ভালোবাসি তা হতে বিচ্ছিন্ন হওয়াই কষ্ট, আমরা যা চাই তা না পাওয়াই কষ্ট।’[৯] জীবনে আনন্দ আছে বটে, কিন্তু গৌতম অভিনিবেশের নিষ্ঠুর পরীক্ষার বিষয়ে পরিণত করার পর গৌতম লক্ষ করলেন, আমাদের সন্তুষ্টি কীভাবে অন্যদের কষ্টে পরিণত হয়। একজনের সমৃদ্ধি সাধারণত অন্য কারও দারিদ্র্য বা বর্জনের ওপর নির্ভরশীল। আমরা যখন কিছু পাই, আমাদের তা সুখী করে। সঙ্গে সঙ্গে সেটা হারানোর উদ্বেগে ভুগতে শুরু করি আমরা। এমনকি দীর্ঘ মেয়াদে আমাদের অসুখী করবে অন্তর দিয়ে জানা থাকা সত্ত্বেও আমরা কাঙ্ক্ষিত বস্তুর সন্ধান করি।
অভিনিবেশ গৌতমকে এই দুঃখ-কষ্টের কারণ আকাঙ্ক্ষা বা বাসনার ব্যাপকতার ব্যাপারেও দারুণভাবে সংবেদনশীল করে তুলেছিল। অহম সর্বগ্রাসী, অবিরাম মানুষ ও অন্য জিনিস গ্রাস করতে চায়। আমরা কখনও কোনও কিছুকে তার আসল রূপে দেখি না। বরং আমরা সেগুলোকে চাই কিনা তারই ভিত্তিতে সেটা রঞ্জিত হয়, আমরা কীভাবে সেটা পাব, বা কেমন করে তা আমাদের জন্যে লাভ বয়ে আনবে। সুতরাং জগৎ সম্পর্কে আমাদের দর্শন লোভ দিয়ে বিকৃত। আমাদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে অন্যদের বাসনার সংঘাত দেখা দিলে প্রয়াশঃই অশুভ ইচ্ছা ও বৈরিতার সৃষ্টি করে এটা। এখন থেকে গৌতম সাধারণভাবে ‘আকাঙ্ক্ষা’ (তানহা)র সঙ্গে ‘ঘৃণা’ (দোসা) শব্দটিকে জুড়ে দেবেন। আমরা যখন বলি, ‘আমি চাই’, প্রায়শঃই তখন অন্য কেউ আমাদের ইচ্ছায় বাধা দিলে বা আমরা যেখানে ব্যর্থ হয়েছি সেখানে সফল হলে নিজেদের ঈর্ষা, হিংসা ও ক্রোধে পূর্ণ অবস্থায় আবিষ্কার করি। মনের এই ধরনের অবস্থা ‘অদক্ষ,’ কারণ আমাদের তা আরও বেশি স্বার্থপর করে তোলে। সুতরাং সহগামী আকাঙ্ক্ষা ও ঘৃণা এভাবে পৃথিবীর বেশিরভাগ ভোগান্তি ও অশুভের যুগ্ম কারণ। আকাঙ্ক্ষা একদিকে আমাদের দীর্ঘস্থায়ী সন্তুষ্টি দেবে না এমন জিনিস ‘আঁকড়ে’ ধরতে বা ‘ছিনিয়ে’ নিতে প্ররোচিত করে। অন্যদিকে, বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আমাদের অবিরাম অসন্তুষ্ট রাখে। মন ও হৃদয়ে একের পর এক বাসনা অধিকার গ্রহণ করছে, এর ফলেই তেমন কিছু পেতে চাইছে। যেমন অন্তহীনভাবে পুনর্জন্মের একটা ধরণ কামনা করছে তারা। এক নতুন ধরনের অস্তিত্ব। এমনকি আমাদের দৈহিক অবস্থানের পরিবর্তন, ভিন্ন কামরায় যাওয়া, নাশতা করা বা হঠাৎ কাজ রেখে কারও সঙ্গে কথা বলতে যাওয়ার মাঝেও বাসনা (তানহা) নিজেকে তুলে ধরে। ঘণ্টায় ঘণ্টায়, মিনিটে মিনিটে এইসব তুচ্ছ আকাঙ্ক্ষা আমাদের আক্রমণ করে, ফলে আমরা বিশ্রাম পাই না। আমরা ভিন্ন কিছু হবার আকর্ষণে নিঃশেষ ও বিক্ষিপ্ত হই। ‘জগতের স্বভাবই পরিবর্তিত হওয়া, অন্য কিছু হওয়ার জন্যে সবসময় প্রতিজ্ঞ সে,’ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন গৌতম। ‘এটা পরিবর্তনের নিয়ন্ত্রণাধীন, কেবল পরিবর্তনের ধারাতেই খুশি হয়। কিন্তু পরিবর্তনের প্রতি এই ভালোবাসা খানিকটা ভয় বহন করে। খোদ এই ভয়ই দুঃখ।[১০]
কিন্তু এই সত্য নিয়ে ভাববার সময় সাধারণ যৌক্তিক উপায় অবলম্বন করেননি গৌতম। এগুলোর সঙ্গে একাত্ম হওয়া লক্ষ্যে যোগের কৌশল অবলম্বন করেছেন তিনি যা এসব সাধারণ বিচারবুদ্ধির ভেতর দিয়ে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তের তুলনায় ঢের স্পষ্ট ও নিবিড়ভাবে সেগুলো যেন স্পষ্ট ও আন্তরিক হয়ে ওঠে। প্রতিদিন দৈনন্দিন খাবারের পক্ষে পর্যাপ্ত ভিক্ষা সংগ্রহের পর, সাধারণত দুপুরের আগেই খেতেন তিনি, একটা নিরিবিলি জায়গা খুঁজে বের করতেন গৌতম। আসন পেতে বসে যোগের একাগ্রতা বা মনোনিবেশের অনুশীলন শুরু করতেন।[১১] যোগের প্রেক্ষিতে অভিনিবেশের অনুশীলন করতেন তিনি। ফলে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি এক নতুন স্পষ্টতা পায়। তিনি ‘সরাসরি’ এগুলো দেখতে পেতেন, প্রবেশ করতেন এবং সেগুলোকে বিকৃতকারী আত্ম-রক্ষাকারী অহমবাদের ছাকুনি ছাড়াই পর্যবেক্ষণ করতে শিখতেন। মানুষ সচরাচর যন্ত্রণার সর্বব্যাপীতা উপলব্ধি করতে চায় না। কিন্তু গৌতম এখন প্রশিক্ষিত যোগির দক্ষতা নিয়ে ‘বস্তুর আসল রূপে’ সেগুলোকে দেখতে শিখছিলেন। তিনি অবশ্য এইসব অধিকতর নেতিবাচক সত্যে থেমে যাননি, বরং একইরকম ঐকান্তি কতায় ‘দক্ষ’ অবস্থারও লালন করছিলেন। কোনও ব্যক্তি, পরে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি, যোগ অনুশীলন করার সময়, পায়ের ওপর পা তুলে বসে প্রাণায়ামের শ্বাস-প্রশ্বাস অনুশীলনের মাধ্যমে সচেতনতার বিকল্প অবস্থা সৃষ্টি করে এইসব ইতিবাচক ও সহায়ক অবস্থার বিকাশ ঘটাতে পারে।
মন থেকে একবার পরশ্রীকাতরতা ও ঘৃণা তাড়াতে পারলে অসৎ ইচ্ছা বিহীন বাস করবে সে, প্রেমময়ও হয়ে উঠবে। সকল জীবিত সত্তার মঙ্গল কামনা করবে। একবার অলসতা ও নিস্পৃহতার মানসিক অভ্যাস ত্যাগ করার পর সে কেবল আলস্য ও নিস্পৃহতা থেকেই মুক্তি পাবে না, বরং এমন একটা মন পাবে যা সাবলীল, নিজের ব্যাপারে সজাগ ও সম্পূর্ণ সতর্ক…একবার উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দূর করার পর উদ্বেগহীন জীবন কাটাবে সে, হয়ে উঠবে শান্ত, অটল…একবার অনিশ্চয়তা দূর করতে পারলে এমন এক মন নিয়ে বাস করবে যা দুর্বলকারী সন্দেহ হতে মুক্ত ও অনুপকারী (অকুসলা) মানসিক অবস্থায় আক্রান্ত হবে না।
এভাবে যোগি তাঁর মনকে ঘৃণা, নিস্পৃহতা, উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা হতে ‘নিষ্কলুষ করে তোলে।’[১২] ব্রাহ্মণরা বিশ্বাস করতেন, পশুবলীর আচরিক কম্ম সম্পাদনের ভেতর দিয়ে তাঁরা এই ধরনের আধ্যাত্মিক পরিশুদ্ধতা অর্জন করেছেন। কিন্তু গৌতম উপলব্ধি করেছিলেন, কোনও পুরোহিতের মধ্যস্থতা ছাড়াই, ধ্যানের মানসিক কম্ম দিয়ে যে কেউই এই পরিশুদ্ধতার বিকাশ ঘটাতে পারে। তিনি বিশ্বাস করতেন, যোগ কৌশলে যথেষ্ট গভীরতায় সম্পাদন করা হলে সচেতন ও অচেতন মনের অস্থির ও বিধ্বংসী প্রবণতাকে পরিবর্তন করতে পারে।
পরবর্তী বছরগুলোয়, গৌতম দাবি করেছেন, তাঁর উদ্ভাবিত যোগ পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের মানুষের জন্ম দিয়েছে যে কিনা আকাঙ্ক্ষা, লোভ ও অহমবাদের অধীনে নয়। এটা, ব্যাখ্যা করেছেন তিনি, খাপ থেকে বের করা তরবারি বা গর্ত থেকে বেরিয়ে আসা সাপের মতো; ‘তরবারি ও সাপ এক জিনিস; কিন্তু খাপ ও গর্ত সম্পূর্ণ আলাদা কিছু।’[১৩] তাঁর ব্যবস্থায় ধ্যান পশুবলীর স্থান দখল করবে। একই সঙ্গে প্রেমের অনুশীলন প্রাচীন শাস্তিমূলক কৃচ্ছ্রতার (তাপস) জায়গা নেবে। প্রেম, দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাঁর, শিক্ষার্থীকে মানুষের এযাবৎ অজানা যাত্রায় প্রবেশের সুযোগ করে দেবে। আলারা কালামের সঙ্গে যোগ অনুশীলনের সময় চারটি পর্যায়ক্রমিক ঝানা পর্যায়ের ভেতর দিয়ে চেতনার উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছাতে শিখেছিলেন গৌতম; প্রতিটি ঘোর যোগিকে বৃহত্তর আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি ও পরিশুদ্ধতা এনে দেয়। এবার তিনি এই চারটি ঝানাকে সম্মিলিতভাবে তাঁর ভাষায় ‘অপরিমেয়’তে রূপান্তরিত করলেন। প্রতিদিনের ধ্যানে ইচ্ছাকৃতভাবে তিনি প্রেমের আবেগকে জাগিয়ে তুলতেন–”ঘৃণার সাথে অপরিচিত বিশাল, বিস্তৃত ও অপরিমেয় অনুভূতি–এবং তাঁকে পৃথিবীর চার কোণে পাঠিয়ে দিতেন। এই হিত সাধনের সংকল্প হতে কোনও কিছুই–গাছ, পশু, দানো, বন্ধু বা শত্রু–কাউকেই বাদ দিতেন না। প্রথম ঝানার অনুরূপ প্রথম ‘অপরিমেয়’তে তিনি সবকিছু ও সবার প্রতি বন্ধুত্বের একটা অনুভুতির বিকাশ ঘটান। এখানে দক্ষতা অর্জনের পর তিনি দ্বিতীয় ঝানার সাহায্যে সহানুভুতির বিকাশ ঘটাতে অগ্রসর হন। অন্য মানুষ ও বস্তুর সঙ্গে কষ্ট ভোগ করতে ও তাদের ব্যথায় সমবেদনা জানানো শেখেন, ঠিক যেমন গোলাপজাম গাছের নিচে ঘাস ও কীটপতঙ্গের কষ্ট অনুভব করেছিলেন। তিনি তৃতীয় ঝানায় পৌঁছানোর পর অন্যের সুখে আনন্দিত হওয়ার ‘প্রেমময় আনন্দের’ লালন করেছেন, সেটা কীভাবে তাঁকে লাভবান করতে পারে তা না ভেবেই। সব শেষে চতুর্থ ঝানা অর্জন করার পর, যেখানে যোগি ধ্যানের বস্তুর সঙ্গে এমনভাবে মিশে যায় সে যন্ত্রণা বা সুখের উর্ধ্বে উঠে যায়, আকর্ষণ বা বৈরিতার কোনও বোধ ছাড়াই গৌতম অন্য সবার প্রতি সামগ্রিক প্রশান্তি আকাঙ্ক্ষা করেন।[১৪] খুব কঠিন একটা পর্যায় ছিল এটা, কেননা এখানে যোগির সেই অহমবাদকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে হয় যা সবসময় অন্য বস্তু বা মানুষ কীভাবে কারও জন্যে সুবিধাজনক বা অসুবিধাজনক হতে পারে সেটা লক্ষ করে। এর জন্যে প্রয়োজন সকল ব্যক্তিগত পছন্দের পরিত্যাগ এবং সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ঔদার্য অবলম্বন। প্রথাগত যোগ যেখানে যোগির মাঝে এমন এক দুর্ভেদ্য স্বাধীনতা গড়ে তুলেছে যাতে করে যোগি ক্রমবর্ধমানহারে জগৎ সম্পর্কে নিস্পৃহ হয়ে পড়ে, সেখানে গৌতম অন্য সকল সত্তার প্রতি পুরোনো অনুশীলনের সঙ্গে প্রেমময় দয়া মিশিয়ে সামগ্রিক সহানুভূতির মধ্য দিয়ে নিজেকে অতিক্রম করে যাওয়া শিখছিলেন।
অভিনিবেশ ও অপরিমেয় উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল সেই অহমবাদের ক্ষমতাকে নিরপেক্ষ করা যা মানুষের সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করে। ‘আমি চাই’ না বলে যোগি অন্যদের মঙ্গল কামনা করতে শেখে: আমাদের আত্ম-কেন্দ্রিক লোভের ফল ঘৃণার কাছে হার স্বীকার না করে গৌতম দয়া ও শুভেচ্ছার এক প্রেমময় আগ্রাসন পরিচালনা করছিলেন। যোগির প্রাবল্যের সঙ্গে এইসব ইতিবাচক, দক্ষ পর্যায়ের বিকাশ ঘটানো হলে আরও সহজে আমাদের মনের অচেতন প্রবণতায় প্রবেশ করে অভ্যাসে পরিণত করবে। ভঙ্গুর অহমকে বাঁচাতে আমরা আমাদের ও অন্যদের ভেতর যেসব বাধা গড়ে তুলি সেগুলোকে ধ্বংস করাই অপরিমেয়র নকশার উদ্দেশ্য: এগুলো সত্তার বৃহত্তর আওতা ও বর্ধিত দিগন্তের সন্ধান করে। মন স্বাভাবিক, স্বার্থপর দৃষ্টিভঙ্গি হতে মুক্ত হয়ে অন্য সকল সত্তাকে আলিঙ্গন করার সময় ‘প্রসারণশীল, সীমাহীন, বর্ধিত, ঘৃণা বা তুচ্ছ বৈরিতামুক্ত’ হওয়ার অনুভূতি জাগে। এখনকার অনুভূত সচেতনতা জগতকে ঘিরে রাখা ‘দক্ষ শাখারির ফু’-এর শব্দের মতোই অসীম মনে হয়। একেবারে উঁচু পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হলে দরদের এই যোগ (করুণা) ‘মনের মুক্তি’ (সেতো-বিমুক্তি) বয়ে আনে, এই পরিভাষাটি পালি টেক্সটে খোদ আলোকপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে।[১৫] অভিনিবেশের অনুশীলনের মাধ্যমেও, বিশেষ করে প্রাণায়ামের সঙ্গে যুক্ত হওয়া অবস্থায় এক গভীরতর প্রশান্তি অনুভব করতে শুরু করেছিলেন গৌতম। আমাদের নিজস্ব প্রয়োজন ও আকাঙ্ক্ষার তুচ্ছ সীমানায় আবদ্ধ করে আমাদের জীবন ও অন্যদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ককে বিষময় করে তোলা স্বার্থপর কামনা হতে মুক্ত অবস্থায় জীবন যাপনের রূপ আবিষ্কার করছিলেন তিনি। এসব উচ্ছৃঙ্খল আকাঙ্ক্ষায় হ্রাসমানহারে প্রভাবিত হচ্ছিলেন। দেখা গেছে, এই ধরনের আত্ম-পর্যালোচনার অভ্যাস বৌদ্ধ অনুশীলনকারীদের আমাদের শান্তি হতে বঞ্চিতকারী বিচ্যুতিসমূহ জরিপে সাহায্য করেছে: ধ্যানী ওইসব হানাদার চিন্তা ও চাহিদার ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতি সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠার সাথে সাথে সেগুলোর সঙ্গে নিজেকে মেলানো বা কোনওভাবে সেগুলোকে ‘আমার’ হিসাবে দেখা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে সেগুলো কম বিঘ্ন সৃষ্টিকারী হয়ে পড়ে।[১৬]
বহু বছরের কৃচ্ছ্রতা সাধনের পর স্বাস্থ্য উদ্ধারে গৌতমের কত দীর্ঘ সময় লেগেছিল আমরা জানি না। ধর্মগ্রন্থগুলো নাটকীয় রূপ দেওয়ার জন্যে প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করছে। ধারণা দিয়েছে যে, গৌতম প্রথম জাউ খাবার পরপরই নিজের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্যে প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিলেন। এটা সত্যি হতে পারে না। অভিনিবেশ ও দক্ষ অবস্থার বিকাশে সময় লাগে। স্বয়ং গৌতম বলেছেন, এতে অন্তত সাত বছর লাগতে পারে। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমায় অলক্ষে নতুন সত্তা গড়ে উঠবে। ‘ঠিক সাগর যেমন ক্রমশঃ ঢালু হয়ে যায়, ধীরে ধীরে দূরে সরে যায়, আর কোনও রকম আকস্মিক খাদ ছাড়াই ক্রমশঃ ঢালু হয়,’ পরে শিষ্যদের সতর্ক করেছেন তিনি, ‘এই পদ্ধতিতেও তেমনি পরম সত্যের আকস্মিক কোনও অনুভূতি ছাড়াই প্রশিক্ষণ, অনুশীলন ও চর্চা ধীর মাত্রায় কার্যকর হয়।’[১৭] টেক্সট দেখায় যে, গৌতম রাতারাতি পরম আলোকপ্রাপ্ত হয়ে বুদ্ধে পরিণত হয়েছেন, কারণ এগুলো ঐতিহাসিক তথ্য নিয়ে নয়, মুক্তি ও অভ্যন্তরীণ শান্তি অর্জন প্রক্রিয়ার সাধারণ বাঁক অনুসন্ধানেই বেশি আগ্রহী।
এভাবে ধর্মগ্রন্থের অন্যতম প্রাচীন অংশে আমরা পড়ি, গৌতম তাঁর পাঁচ সঙ্গী কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছিলেন। প্রথম খাদ্য গ্রহণের পর পরিপুষ্ট হয়ে সহজভাবেই উরুবেলার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলেন তিনি, নিরঞ্জর নদীর পাশে সেনানীগামায় পৌঁছার পর ‘পছন্দসই একটুকরো জমিন, একটা মুগ্ধকর বন, চমৎকার মসৃণ তীর অলা একটা নদী এবং একটা গ্রাম, যে গ্রামের অধিবাসীরা তাকে খাওয়াবে,’[১৮] লক্ষ করলেন। গৌতম ভাবলেন, এটাই চূড়ান্ত প্ৰয়াস গ্রহণের উপযুক্ত জায়গা, যা তাঁকে আলোকপ্রাপ্তি এনে দেবে। গোলাপজাম গাছের নিচের সেই অনায়াস প্রথম ঝানায় পৌঁছে দেওয়ার মতো প্রশান্ত সন্তুষ্টির পুনর্নির্মাণ করতে হলে ধ্যানের জন্যে একটা জুৎসই স্থান খুঁজে পাওয়ার প্রয়োজন ছিল। ট্র্যাডিশন বলছে, একটা বোধি বৃক্ষের নিচে বসে নিব্বানা লাভ না করা পর্যন্ত জায়গা না ছাড়ার শপথ নিয়ে আসন গ্রহণ করেন তিনি। মনোরম সেই বন এখন তীর্থযাত্রার গুরুত্বপূর্ণ স্থান বোধ গয়া নামে পরিচিত, কারণ মনে করা হয় এখানেই গৌতম যথাভূতো–আলোকন বা জাগ্রত হওয়ার অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন।
বসন্তের শেষ সময় ছিল সেটা। পণ্ডিতগণ সাধারণত গৌতমের আলোকপ্রাপ্তির সময়কে মোটামুটি বিসিই ৫২৪ সাল নির্ধারণ করেছেন, যদিও কেউ কেউ পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে আরও পরের সময়ের পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। সে রাতে কী ঘটেছিল সে সম্পর্কে পালি টেক্সট আমাদের কিছু তথ্য যোগায়, কিন্তু বৌদ্ধদের নিয়ম কানুনের অভিজ্ঞতাহীন কারও কাছে এসব তেমন অর্থ বহন করে না। এসব তথ্য জানায় যে, আমাদের জানা সকল জীবনের শর্তাধীন প্রকৃতি নিয়ে ভেবেছেন গৌতম, নিজের গোটা অতীত জীবন দেখতে পেয়েছেন, এবং তারপর সেই ছেলেবেলার ‘বিচ্ছিন্ন’ ও নিঃসঙ্গ অবস্থা নতুন করে আবিষ্কার করেছেন। এরপর অনায়াসে প্রথম ঝানায় প্রবেশ করেছেন তিনি এবং তারপর ক্রমান্বয়ে উচ্চতর পর্যায় হয়ে তাঁকে চিরতরে বদলে দেওয়া অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে চেতনার এমন অবস্থায় পৌঁছে গেছেন যা তাঁর মনে বিশ্বাস জাগিয়েছে, নিজেকে সামসারা ও পুনর্জন্মের চক্র হতে মুক্ত করেছেন তিনি।[১৯] কিন্তু ঐতিহ্যগতভাবে চার মহান সত্যি হিসাবে পরিচিত ও বুদ্ধ মতবাদের মৌল শিক্ষা হিসাবে বিবেচিত এই অন্তর্দৃষ্টির বেলায় তেমন নতুনত্ব আছে মনে হয় না। এই বৈচিত্র্যের প্রথমটি হচ্ছে সমগ্র মানব জীবন ঘিরে থাকা ভোগান্তির (দুঃখ) মহান সত্যি। দ্বিতীয় সত্য হচ্ছে, এই ভোগান্তির কারণ আকাঙ্ক্ষা (তানহা)। তৃতীয় মহান সত্যে গৌতম জোর দিয়ে বলেছেন, এই বিপত্তি হতে উদ্ধারের উপায় হিসাবে নিব্বানার অস্তিত্ব এবং সব শেষে, তিনি নিব্বানার পর্যায়ে দুঃখকষ্ট ও বেদনা হতে অবসানের দিকে চলে যাওয়া পথের সন্ধান লাভ করার দাবি করেছেন।
এইসব সত্যের কোনও অসাধারণ মৌলিকত্ব আছে বলে মনে হয় না। উত্তর ভারতীয় বেশিরভাগ সাধু-সন্ন্যাসী প্রথম তিনটির সঙ্গে একমত হতো। গৌতম স্বয়ংও তাঁর অনুসন্ধানের একেবারে গোড়া হতে এগুলোর সত্যতায় বিশ্বাসী ছিলেন। নতুন কিছু থাকলে সেটা চতুর্থটি, যেখানে গৌতম আলোকনের পথ পাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। মহান অষ্টশীলা পথ। এর আটটি উপাদানকে নৈতিকতা, ধ্যান এবং প্রজ্ঞার সমন্বয়ে তিন পর্যায়ের কর্মধারায় অধিকতর যৌক্তিকীকরণ করা হয়েছে।
[১] নৈতিকতা (শিলা): সত্য কথন, সত্য কর্ম এবং সঠিক জীবিকা যার অন্তর্ভূক্ত। এখানে আমাদের আলোচনা অনুযায়ী ‘দক্ষ’ অবস্থার বিকাশ সাধন আবশ্যিকভাবে জড়িত।
[২] ধ্যান (সমাধি): সঠিক প্রয়াস, অভিনিবেশ ও মনোসংযোগের অধীনে গৌতমের পরিমার্জিত যোগ অনুশীলন এর অন্তর্ভূক্ত।
[৩] প্রজ্ঞা (পান্না): সঠিক উপলব্ধি ও সঠিক সিদ্ধান্তের দুটি গুণ শিক্ষার্থীকে নৈতিকতা ও ধ্যানের সাহায্যে বুদ্ধের ধম্মকে উপলব্ধি, প্রত্যক্ষভাবে প্রবেশ ও একে পরবর্তী অধ্যায়ে আমাদের আলোচনা অনুযায়ী তার জীবনে আত্মস্থ করতে সক্ষম করে তোলে।
বোধ গয়ায় রাতারাতি গৌতমের আলোকপ্রাপ্তির কাহিনীতে কোনও সত্যি থেকে থাকলে সেটা এমন হতে পারে যে, তিনি সহসা এমন একটা পদ্ধতি আবিষ্কারের ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চয়তা লাভ করেছিলেন যা সউদ্যমে অনুসরণ করলে একজন নিবিষ্ট সন্ধানীকে নিব্বানায় পৌঁছে দেবে। তিনি এটা নিৰ্মাণ করেননিঃ এটা তাঁর নতুন সৃষ্টি বা উদ্ভাবন ছিল না। উল্টো, তিনি সবসময়ই জোর দিয়ে ‘সুপ্রাচীন কালের একটা পথ আবিষ্কারের’ কথা বলেছেন যে পথে ‘বহুযুগ আগের মানুষ চলাচল করেছে।’[২০] তাঁর পূর্বসুরি অন্য বুদ্ধগণ গণনার অতীত দীর্ঘদিন আগে এই পথের শিক্ষা দিয়েছিলেন, কিন্তু এই প্রাচীন জ্ঞান বছর পরিক্রমায় ম্লান হয়ে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে। গৌতম জোর দিয়ে বলেছেন, এই দর্শন স্রেফ বস্তুর ‘প্রকৃত রূপের’ বিবরণ; অস্তিত্বের মূল কাঠামোতেই এই পথের উপস্থিতি। সুতরাং এটাই ধম্ম-এর সর্বোচ্চ রূপ, কারণ তা বিশ্ব জগতের জীবনধারা পরিচালনাকারী মৌলিক নীতিমালা ব্যাখ্যা করে। এপথে থাকলে নারী-পুরুষ, পশুপাখী ও দেবতাদের সবাইই আলোকপ্রাপ্ত হতো যা এনে দিত শান্তি ও সম্পূর্ণতা, কারণ তখন আর তারা তাদের গভীরতম উপাদানের বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত থাকত না।
কিন্তু এটা অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে চারটি মহান সত্যিকে কেবল যৌক্তিক বুদ্ধিমত্তা দিয়ে যাচাই করা যাবে নাঃ এগুলো স্রেফ কল্পিত বৈচিত্র্য নয়। বুদ্ধের ধম্ম আবশ্যিকভাবে একটা পদ্ধতি। কেবল অধিবিদ্যিক সূক্ষ্মতা কিংবা বৈজ্ঞানিক নির্ভুলতার কারণেই এটা সফল বা ব্যর্থ হয় না, বরং কতদূর পর্যন্ত কাজ করছে তার ওপর নির্ভর করে। সত্যসমূহ দুঃখ-কষ্টের সমাপ্তি আনে বলে দাবি করা হয়, সেটা মানুষ কোনও পরিত্রাণমূলক বিশ্বাসে বা নির্দিষ্ট বিশ্বাসে আস্থা স্থাপন করে বলে নয়, বরং তারা গৌতমের কর্মধারা বা জীবন ধারা অবলম্বন করে বলে। শত শত বছরের পরিক্রমায় নারী-পুরুষ প্রকৃতপক্ষেই এইসব নিয়ম-কানুন এক ধরনের শান্তি ও অন্তর্দৃষ্টি এনে দিয়েছে বলে আবিষ্কার করেছে। অ্যাক্সিয়াল যুগের অন্য সকল সাধুদের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত বুদ্ধের দাবি ছিল যে, নিজেকে অতিক্রম করে এক দুৰ্জ্জেয় সত্তায় পৌঁছানোর মাধ্যমে যৌক্তিক উপলব্ধি ছাপিয়ে নারী-পুরুষ পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে ওঠে। বুদ্ধ কখনও চারটি সত্যের জ্ঞান অনন্য সাধারণ বলে দাবি করেননি। কিন্তু বর্তমান কালে তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি এসব ‘উপলব্ধি’ করতে পেরেছেন ও সেগুলোকে নিজ জীবনে বাস্তবায়িত করতে পেরেছেন। আকাঙ্ক্ষা, ঘৃণা ও অজ্ঞতাকে ধ্বংস করেছেন বলে আবিষ্কার করেছেন, মানুষকে যা বন্দি করে রাখে। নিব্বানা অর্জন করেছিলেন তিনি। যদিও এখনও শারীরিক অসুস্থতা ও অন্যান্য উত্থান-পতনের শিকার হন তিনি, কিন্তু তাই বলে কোনও কিছুই তাঁর অন্তস্থ-শান্তিকে স্পর্শ করতে পারবে না কিংবা গুরুতর মানসিক পীড়ার কারণ হবে না। তাঁর পদ্ধতি কাজে এসেছে। বোধি বৃক্ষের নিচে সেই গুরুত্বপূর্ণ রাতের শেষে বিজয়ীর সুরে চিৎকার করে উঠেছিলেন তিনি, ‘পবিত্র জীবন শেষ পর্যন্ত যাপন করা হয়েছে! যা করার ছিল, সম্পাদন করা হয়েছে। আর কিছু করার নেই।’[২১]
আমরা যারা নৈতিকতা ও ধ্যানের বৌদ্ধ কর্মসূচি অনুযায়ী চলি না তাদের পক্ষে এই দাবি যাচাই করার কোনও উপায় নেই। বুদ্ধ বরাবর পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে, স্রেফ যৌক্তিক চিন্তা দিয়ে তাঁর ধম্ম বোঝা যাবে না। কেবল যোগি পদ্ধতিতে ও সঠিক নৈতিক পটভূমিতে ‘প্রত্যক্ষভাবে’ বুঝতে পারলেই তা আসল তাৎপর্য নিয়ে প্রকাশিত হয়।[২২] চারটি মহান সত্যি যৌক্তিক অর্থ প্রকাশ করে বটে, কিন্ত শিক্ষার্থী এক গভীর স্তরে সেগুলোর সঙ্গে একাত্ম হয়ে সেগুলোকে নিজ জীবনে আত্মস্থ না করা পর্যন্ত তা আবশ্যক হয়ে ওঠে না। তখন, একমাত্র তখনই সে ‘মহাউল্লাস,’ ‘আনন্দ’ ও ‘প্রশান্তি’ অনুভব করবে। পালি টেক্সট অনুযায়ী আমরা আমাদের অহমবাদ বিসর্জন দিলে, আত্মকেন্দ্রিকতা হতে নিজেদের মুক্ত করলে ও সত্যকে ‘তার আসল রূপে’ প্রত্যক্ষ করলে আমাদের কাছে তা ধরা দেয়।[২৩] বুদ্ধের নির্দেশিত ধ্যান ও নৈতিকতা বাদে সত্যি সঙ্গীতের মতোই বিমূর্ত রয়ে যায়, আমাদের বেশিরভাগই কাগজের পাতায় তার আসল সৌন্দর্য ধরতে পারি না, বরং কোনও দক্ষ শিল্পীর বাদন ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়।
যদিও সত্যিসমূহ যৌক্তিক অর্থ প্রকাশ করে, কিন্তু টেক্সট জোর দেয় যে, যৌক্তিক প্রক্রিয়ায় এগুলো গৌতমের কাছে ধরা দেয়নি। বোধি বৃক্ষের নিচে বসে ধ্যান করার সময় যেন তাঁর সত্তার গভীরতা হতে তাঁর মাঝে ‘জেগে উঠেছে’। তিনি ‘আন্তরিকতা, উৎসাহ ও আত্মনিয়ন্ত্রণে’র ভেতর দিয়ে যোগ অনুশীলন চর্চাকারী যোগির অর্জিত ‘প্রত্যক্ষ জ্ঞানের’ মতো কিছুর সাহায্যে নিজের ভেতর উপলব্ধি করেছেন। গৌতম এমন নিবিড়ভাবে তাঁর ধ্যানের লক্ষ্য এইসব সত্যির মাঝে নিমগ্ন ছিলেন যে, কোনও কিছুই এগুলো ও তাঁর হৃদয়- মনের মাঝখানে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। মানুষ যখন তাঁর মতো আচরণ করে এবং ঘটনার প্রতি সাড়া দেয়, ধম্মের রূপ দেখতে পায় তারা, মানবীয় রূপে নিব্বানার দেখা পায়। গৌতমের অভিজ্ঞতার স্বাদ পেতে হলে আমাদেরকে সম্পূর্ণ আত্ম-পরিত্যাগের চেতনায় সত্যির দিকে অগ্রসর হতে হবে। আমাদেরকে আমাদের পুরোনো অজাগ্রত সত্তাকে পেছনে ফেলে যেতে প্রস্তুত থাকতে হবে। শিক্ষাব্রতী সব রকম অহমবাদ দূরে ঠেলে দিতে তৈরি থাকলেই কেবল গৌতম আবিষ্কৃত প্রেমময় নৈতিকতা ও যোগ মুক্তি এনে দেবে। এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, বোধি বৃক্ষের নিচে নিব্বানা লাভের মুহূর্তে গৌতম ‘আমি মুক্ত বলে চেঁচিয়ে ওঠেননি, বরং বলেছেন ‘এটা মুক্তি পেয়েছে।[২৪] নিজেকে ছাড়িয়ে গেছেন তিনি। এক ধরনের exstasis অর্জন করেছেন। নিজের মানবীয় সত্তার এক পরিবর্ধিত ‘অপরিমেয়’ মাত্রা আবিষ্কার করেছেন, যার কথা তাঁর আগে জানা ছিল না।
বসন্তের সেই রাতে নিব্বানা লাভের দাবি করে কী বুঝিয়েছিলেন নতুন বুদ্ধ? তিনি স্বয়ং কি শব্দের অর্থ অনুযায়ী মোমবাতির শিখার মতো ‘নিভে গিয়েছিলেন’? ছয় বছর ব্যাপী অন্বেষণকালে গৌতম মর্ষকামীর মতো নিশ্চিহ্নতাকে আমন্ত্রণ জানাননি, আলোকনের সন্ধান করেছেন তিনি। মানুষ হিসাবে আপন সম্ভাবনার পূর্ণতায় জাগ্রত হতে চেয়েছেন। নিভে যেতে চাননি 1 নিব্বানা ব্যক্তিগত বিলুপ্তি বোঝায়নি, ব্যক্তিত্ব নয়, নিভে গিয়েছিল তাঁর লোভ, ঘৃণা ও কুহকের অগ্নিশিখা। ফলে এক আশীর্বাদময় ‘শীতলতা’ ও শান্তি বোধ করেছেন তিনি। মনের ‘অসহায়ক’ অবস্থাগুলোকে চাপা দিয়ে বুদ্ধ স্বার্থহীনতা হতে উদ্ভুত শান্তি অর্জন করেছেন। এটা এমন একটা অবস্থা যা আমরা যারা এখনও আমাদেরকে অন্যের প্রতি বৈরী করে তোলা ও আমাদের দৃষ্টিকে বিকৃতকারী অহমবাদের আকাঙ্ক্ষায় বিজড়িত তাদের পক্ষে কল্পনা করা সম্ভব নয়। সেজন্যেই আলোকপ্রাপ্তির পরবর্তী বছরগুলোয় বুদ্ধ সবসময় নিব্বানাকে সংজ্ঞায়িত বা বর্ণনা করতে অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, তেমন কিছু করাটা ‘অসঙ্গত’ হবে, কারণ অনালোকিত কোনও মানুষের কাছে এমন একটা অবস্থার বর্ণনা দেওয়ার উপযোগি কোনও শব্দ নেই।[২৫] নিব্বানা লাভের অর্থ এমন ছিল না যে বুদ্ধ আর কখনওই দুঃখ-কষ্ট বোধ করবেন না। তিনি বৃদ্ধ হবেন, অসুস্থ হয়ে আর সবার মতোই মারা যাবেন এবং এসব ক্ষেত্রে কষ্ট পাবেন। নিব্বানা জাগ্রত ব্যক্তিকে ঘোরের মতো নিষ্কৃতি দেয় না, বরং দুঃখ- কষ্টের মাঝে এমন এক অন্তস্থ আশ্রয় যোগায় যা নারী ও পুরুষকে কষ্টের সঙ্গে মানিয়ে নিতে, একে আয়ত্ত করতে, নিশ্চিত করতে ও গভীর মানসিক স্তরে শান্তি অনুভব করতে শেখায়। সুতরাং, যে কারও মাঝেই, প্রত্যেকের সত্তার একান্ত গভীরে নিব্বানার দেখা মেলে। এটা নেহাতই স্বাভাবিক একটা অবস্থা, কোনও অতিলৌকিক ত্রাতা আমাদের জন্যে অর্জন করেননি বা কারও করুণায় অবতীর্ণ হয়নি। গৌতমের মতো একাগ্রতার সঙ্গে আলোকনের পথের বিকাশ ঘটালে যে কেউ এটা অর্জন করতে পারে। নিব্বানা এক অটল কেন্দ্র; এটা জীবনকে অর্থ দেয়। যারা এই প্রশান্ত স্থানের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলে ও এই লক্ষ্যে জীবন পরিচালিত করে না, তারা ভেঙে পড়তে পারে। শিল্পী, কবি, সঙ্গীত শিল্পী কেবল শান্তি ও শুদ্ধতার এই অন্তস্থ কেন্দ্রে পৌঁছানোর সুযোগ পেলে তখন সে আর সংঘাতময় আতঙ্ক ও আকাঙ্ক্ষায় পরিচালিত হয় না, প্রশান্তির সঙ্গে বেদনা, বিষাদ ও শোক মোকাবিলা করতে পারে। একজন আলোকপ্রাপ্ত বা জাগ্রত মানুষ নিজের মাঝে এক শক্তি আবিষ্কার করেছে যা স্বার্থপরতার নাগালে বাইরে যথাযথভাবে স্থাপিত সত্তা হতে উদ্ভূত।
একবার শান্তির এই অস্তস্থ বলয়, অর্থাৎ নিব্বানার দেখা পাবার পর, গৌতম পরিণত হয়েছিলেন বুদ্ধে। অহমবাদের বিনাশ ঘটাতে পারলে নতুন অস্তিত্ব জাগিয়ে তোলার মতো শিখা বা জ্বালানি থাকবে না, এব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন তিনি, কারণ তাঁকে সামসারার সঙ্গে বন্ধনে জড়িতকারী আকাঙ্ক্ষার পুরোপুরি বিনাশ ঘটেছে। মৃত্যুর পর পরিনিব্বানা, চূড়ান্ত বিশ্রাম লাভ করবেন তিনি। তবে অনেক সময় পশ্চিমাবাসীরা যেমন মনে করে, এটা সম্পূর্ণ বিলুপ্তি বোঝায়নি। পরিনিব্বানা এক ধরনের অস্তিত্ব নিজেরা আলাকপ্রাপ্ত না হলে আমরা যা বুঝতে পারব না। এর বর্ণনা দেওয়ার মতো কোনও ভাষা বা তত্ত্ব নেই, কারণ আমাদের ভাষা উদ্ভুত হয়েছে আমাদের অসুখী জাগতিক অস্তিত্বের ইন্দ্রিয়জ উপাত্ত হতে; অহমবাদের অস্থিত্বহীন একটা জীবনের কল্পনা করতে পারি না আমরা। কিন্তু তাই বলে তেমন একটা অস্তিত্ব অসম্ভব বোঝায় না। মৃত্যুর পর একজন আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি আর অস্তিত্বশীল থাকবে না বিশ্বাস করা বৌদ্ধ বিশ্বাসের পরিপন্থী।[২৬] একইভাবে একেশ্বরবাদীরা জোর দিয়ে বলেছে, যে সত্তাকে তারা ‘ঈশ্বর’ নামে ডাকে তাঁর যথার্থ বর্ণনা দেওয়ার মতো কোনও ভাষা নেই। পরবর্তী জীবনে বুদ্ধ তাঁর শিষ্যদের বলবেন, ‘চূড়ান্ত বিশ্রামে (পরিনিব্বানা) গমনকারীকে কোনওভাবে সংজ্ঞায়িত করা যাবে না। তাকে বর্ণনা করার মতো কোনও ভাষা নেই। চিন্তা যা ধরতে পারত তা বাতিল হয়ে গেছে, তেমনি সবধরনের ভাষাও।’[২৭] একেবারে জাগতিক ভাষায় নিব্বানা ‘কিছু না’, সেটা অস্তিত্বহীন বলে নয়, বরং তা আমাদের জানা কোনও কিছুর সঙ্গে মেলে না বলে। কিন্তু যারা যোগ অনুশীলন ও প্রেমময় নৈতিকতার মাধ্যমে আপন সত্তায় অটল কেন্দ্রের সন্ধান পেয়েছে তারা অপরিমেয় সমৃদ্ধ সত্তার দেখা লাভ করেছে, কারণ অহমবাদের সীমাবদ্ধতা ছাড়া বাঁচতে শিখেছে তারা।
পালি টেক্সটে বর্ণিত বোধি বৃক্ষের নিচে বুদ্ধের আলোকপ্রাপ্তির বিবরণ আধুনিক পাঠককে হতবুদ্ধি ও হতাশ করতে পারে। দক্ষ যোগি নয় এমন মানুষের কাছে থেরাভেদীয় ধর্মগ্রন্থগুলো যেসব ক্ষেত্রে অস্পষ্ট হয়ে গেছে, এটা তেমনি একটা; কারণ ধ্যানের কৌশলাদি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এখানে। নিদান কথা নামের পরবর্তী কালের ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত কাহিনী বহিরাগত কারও কাছে অধিকতর সহায়ক, যা আলোকনের ধারণাকে সাধারণ মরণশীলের পক্ষে অধিকতর বোধগম্য করে তুলেছে। গৌতমের ‘অগ্রসর হওয়া’র কাহিনীর মতোই এখানে এমনভাবে আলোকনের মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক তাৎপর্যের সন্ধান করা হয়েছে যে একজন সাধারণ মানুষ বা বৌদ্ধ শিক্ষব্রতী বুঝতে পারবে। এখানে কোনও যোগ পরিভাষা নেই। আমাদের কাছে আলোকনের সম্পূর্ণ পৌরাণিক বর্ণনা দেয়। লেখক আমাদের ধারণা অনুযায়ী ইতিহাস রচনার প্রয়াস পাচ্ছেন না, বরং নিব্বানার আবিষ্কারে কী জড়িত ছিল দেখাতে সময়হীন ইমেজারি অঙ্কন করেছেন। মিথলজির সাধারণ মটিফ ব্যবহার করেছেন তিনি, যা মনের অভ্যন্তরীণ পথের সন্ধান এবং অসচেতন মনের আবছা জগৎকে স্পষ্টতর করে তোলার জন্যে মনস্তত্ত্বের প্রাক-আধুনিক রূপ হিসাবে চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। বৌদ্ধ মতবাদ আবশ্যিকভাবে মনস্তাত্ত্বিক ধর্ম। সুতরাং, এটা বিস্ময়কর নয় যে, প্রাচীন বৌদ্ধ লেখকগণ মিথোলজির এমন সুদক্ষ প্রয়োগ দেখিয়েছেন।[২৮] আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে এইসব টেক্সটের কোনওটাই কিন্তু আসলে কী ঘটেছিল তা জানাচ্ছে না বরং শ্রোতাকে তার নিজস্ব আলোকপ্রাপ্তিতে সাহায্য করতে চেয়েছে।
নিদান কথা সাহস ও প্রতিজ্ঞার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিচ্ছে; এটা দেখাচ্ছে গৌতম নিজের মাঝে নিব্বানা অর্জনের বাধা সৃষ্টিকারী সকল শক্তির বিরুদ্ধে এক বীরত্বসূচক সংগ্রামে লিপ্ত। আমরা পড়েছি, জাউ খাওয়ার পর মুক্তি লাভের শেষ প্রয়াস চালাতে সিংহের মতো রাজকীয় ভঙ্গিতে বোধি বৃক্ষের দিকে এগিয়ে গেছেন গৌতম। সেইরাতেই লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। প্রথমে নিব্বানা অর্জনের সময় পূর্ববর্তী বুদ্ধগণ কোথায় বসেছিলেন জানার জন্যে গাছটার চারপাশে চক্কর দিয়েছেন তিনি। কিন্তু তিনি যেখানেই দাঁড়িয়েছেন দেখেছেন, ‘বিশাল জমিন ওঠা-নামা করছে, যেন একটা বিশাল ঠেলাগাড়ির চাকা কেন্দ্রের ওপর পড়ে আছে এবং কেউ ওটার কিনারা বরাবর হাঁটছে।[২৯] অবশেষে গাছের পুব দিকে এগিয়ে গেলেন গৌতম। সেখানে দাঁড়াতেই জমিন স্থির হয়ে গেল। গৌতম সিদ্ধান্তের পৌঁছলেন, নিশ্চয়ই এটা সেই ‘নিশ্চল স্থান’ যেখানে অতীতের বুদ্ধগণ অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। সুতরাং ভোরের অঞ্চল পুবদিকে ফিরে আসন পেতে বসলেন তিনি। মনে দৃঢ় প্রত্যাশা, মানুষের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা ঘটাতে যাচ্ছেন। ‘দেহের রক্ত-মাংসসহ আমার ত্বক, পেশি, হাড় শুকিয়ে যাক। আমি মেনে নেব!’ শপথ নিলেম গৌতম। ‘কিন্তু পরম ও চূড়ান্ত প্রজ্ঞা অর্জন না করে এখান থেকে নড়ব না।[৩০]
গৌতম গাছ ঘিরে চক্কর দেওয়ার সময় পৃথিবীর বিচিত্র কম্পনের ওপর জোর দিয়ে টেক্সট আমাদের এই কাহিনী আক্ষরিক অর্থে পাঠ না করার কথা মনে করিয়ে দিয়েছে। এটা কোনও বাস্তব স্থান নয়; মহাজগতের অক্ষে দাঁড়ানো জগৎ-বৃক্ষ নিষ্কৃতির পুরাণের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এখানেই স্বর্গীয় শক্তি পৃথিবীতে আসে। সেখানে মানুষ পরমের দেখা পায় ও পরিপূর্ণতায় এক হয়ে যায়। আমাদের শুধু মনে রাখতে হবে, ক্রিশ্চান কিংবদন্তী অনুযায়ী জেসাসের ক্রস স্বর্গোদ্যানের জ্ঞান ও পাপ বৃক্ষের মতোই একই জায়গায় অবস্থিত। কিন্তু বৌদ্ধ মিথে ঈশ্বর-মানুষ নন বরং মানুষ গৌতমই গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় বসেছিলেন, কারণ মানুষকে অবশ্যই অতিলৌকিক সাহায্য ছাড়াই আত্মরক্ষা করতে হবে। টেক্সট এটা পরিষ্কার করে দিচ্ছে যে, গৌতম মহাবিশ্বের অক্ষে, সমগ্র সৃষ্টি জগতকে ধরে রাখা কিংবদন্তীর কেন্দ্রে পৌঁছেছেন। এই ‘নিশ্চল স্থান’ সেই মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা যা আমাদের জগৎ ও নিজেদের নিখুঁত ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থায় দেখতে সক্ষম করে তোলে। মনস্তাত্ত্বিক স্থিতিশীলতা ও সঠিক পরিচিতি ছাড়া আলোকন অসম্ভব; সেকারণেই সকল বুদ্ধকে–মনের এই অবস্থা অর্জনের জন্যে-নিব্বানা অর্জনে সফল হয়ে ওঠার আগে এখানেই আসন গ্রহণ করতে হয়েছে। এটাই সেই মান্দি অক্ষ, নিশ্চল বিন্দু যেখানে বহু বিশ্ব কিংবদন্তীতে মানুষ বাস্তব ও অনিয়ন্ত্রিতের মোকাবিলা করেছে। এটাই সেই ‘স্থান’ সেখানে সমস্ত কিছু জাগতিক বিশ্বে বিপরীত মনে হওয়া জীবন ও মৃত্যু, শূন্যতা ও প্রাচুর্য, লৌকিক ও অলৌকিক চাকার কেন্দ্রে এসে স্পোকের মতো স্বাভাবিক সচেতনতায় অকল্পনীয় coincidentia oppositorum-এ মিলিত হয়ে পবিত্রতার অনুভূতি সৃষ্টি করে।[৩১] গৌতম যখন ছেলেবেলোয় গোলাপজাম গাছের নিচের অনুরূপ নিখুঁত ভারসাম্যে পৌঁছেছিলেন, যখন তাঁর সমস্ত ইন্দ্ৰিয় একাগ্র হয়ে উঠেছে, তাঁর অহমবাদ নিয়ন্ত্রণাধীনে আসার পরেই, তাঁর বিশ্বাস মতো তিনি ‘অটল স্থানে’ বসতে তৈরি হয়েছিলেন। অবশেষে পরম আলোক গ্রহণের পর্যায়ে পৌঁছেছিলেন তিনি।
কিন্তু সংগ্রাম তখনও শেষ হয়নি। গৌতমকে তাঁর অজাগ্রত জীবন আঁকড়ে থাকা ও বিদায় নিতে অস্বীকৃতি জানানো অবশিষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছে। গৌতমের ছায়া-সত্তা মারা বিশাল সেনাদল সজ্জিত নিয়ে বিশ্ব শাসক চক্কবত্তীর রূপ ধরে তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। স্বয়ং মারা ১৪০ লীগ উঁচু একটা হাতির পিঠে আসীন। ১০০০ হাত গজিয়েছে তাঁর, প্রত্যেক হাতে মারাত্মক সব অস্ত্র দেখা যাচ্ছে। মারা নামের অর্থ কুহক। আমাদেরকে আলোকন থেকে দূরে ঠেলে রাখা অজ্ঞতাকেই তুলে ধরেন, কারণ চক্কবত্তী হিসাবে কেবল শারীরিক শক্তি দিয়ে অর্জন সম্ভব বিজয়ের দেখা পান তিনি তখনও পুরোপুরি আলোকপ্রাপ্ত হননি গৌতম। ফলে করুণার মাধ্যমে সাড়া দেওয়ার চেষ্টা করলেন তিনি। নিজের অর্জিত গুণাবলীকে তরবারি বা বর্মের মতো এই মারাত্মক বাহিনীকে ধ্বংস করে দেওয়ার মতো আত্মরক্ষামূলক অস্ত্র মনে করেছিলেন।[৩২] কিন্তু আমাদের লেখক বলে যাচ্ছেন, মারার প্রতাপ সত্ত্বেও গৌতম ‘অপরাজেয় অবস্থানে’ বসেছিলেন, অমন অশ্লীল নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রমাণ। মারা তাঁর উদ্দেশে নয়টি ভীতিকর ঝড় প্রেরণ করার পরেও অটল রইলেন গৌতম। গৌতমের আলোকপ্রান্তি প্রত্যক্ষ করার জন্যে তাঁর পাশে জড়ো হওয়া দেবতাগণ আতঙ্কে পালিয়ে গেলেন। একা রয়ে গেলেন তিনি। বৌদ্ধ দর্শন অনুযায়ী মুক্তি সন্ধান করার সময় নারী-পুরুষের স্বর্গীয় সাহায্য প্রত্যাশা করার উপায় নেই।
এ পর্যায়ে মারা গৌতমের কাছে এসে অদ্ভুত কথোপথনে ব্যস্ত করে রাখলেন। গৌতমকে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে বললেন, ‘ওটা তোমার নয়, আমার।’ মারা ভেবেছিলেন গৌতম জগৎ ছাড়িয়ে গেছেন, সকল বাহ্যিক বিরোধিতায় অনাক্রান্ত হয়ে গেছেন। কিন্তু মারা এই জগতের অধিশ্বর, চক্কবত্তী হিসাবে ওই গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বসার অধিকার তারই। কিন্তু তিনি বুঝতে পারেননি, এই মাত্র দেখানো তাঁর ক্রোধ, ঘৃণা ও সহিংসতা তাঁকে বোধি বৃক্ষের নিচে অবস্থান গ্রহণের অযোগ্য করে তুলেছে। কেবল যারা সহানুভূতিময় জীবন যাপন করে এ শুধু তাদেরই অধিকার। গৌতম যুক্তি দেখালেন যে, মারা আলোকনের পক্ষে মোটেই প্রস্তুত নন। তিনি কখনও কোনওরকম আধ্যাত্মিক প্রয়াস চালাননি, কখনও দান করেননি, যোগ অনুশীলন করেননি। তো, উপসংহার টানলেন গৌতম, ‘এই আসন তোমার নয়, বরং আমার।’ তিনি আরও যোগ করলেন, পূর্ববর্তী জীবনে তিনি সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়েছেন, এমনকি অন্যের জন্যে নিজের জীবনও বিসর্জন দিয়েছেন। মারা কী করেছেন? তিনি এমন এমন দয়াময় কাজ করার কোনও প্রমাণ হাজির করতে পারবেন? সঙ্গে সঙ্গে মারার সেনাদল সমস্বরে চিৎকার করে উঠল: ‘আমি সাক্ষী!’ বিজয়ীর ঢঙে গৌতমের দিকে ফিরলেন মারা, নিজ দাবির প্রমাণ রাখতে বললেন তাঁকে।[৩৩]
কিন্তু গৌতম ছিলেন একা। আলোকনের জন্যে দীর্ঘ প্রস্তুতির প্রমাণ রাখার মতো কোনও মানুষ বা দেবতা ছিলেন না তাঁর পাশে। হাত বাড়িয়ে সামনের জমিন স্পর্শ করে পৃথিবীকেই তাঁর অতীতের সহানুভুতিসূচক কর্মকাণ্ডের পক্ষে সাক্ষী দেওয়ার আবেদন জানালেন তিনি। প্রচণ্ড গর্জনে চিৎকার করে উঠল পৃথিবী: ‘আমি তোমার সাক্ষী!’ আতঙ্কে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল মারার হাতি। সৈন্যরা আতঙ্কে দৌড়ে দিকবিদিক সটকে গেল।[৩৪] পৃথিবীর সাক্ষীর ভঙ্গি, যেখানে বুদ্ধকে পদ্মাসনে বসে জমিনের দিকে ডান হাত বাড়ানো ভঙ্গিতে থাকতে দেখা যায়, বৌদ্ধ শিল্পকলার একটা প্রিয় আইকন। এটা কেবল মারার নির্জীব পৌরুষের বিরুদ্ধে গৌতমের প্রত্যাখ্যানই দেখায় না, বরং এই গভীর যুক্তি তুলে ধরে যে, বুদ্ধ প্রকৃতই পৃথিবীর মানুষ। ধম্ম কষ্টকর হলেও প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়। পৃথিবীর সাথে নিঃস্বার্থ মানুষের রয়েছে এক গভীর সখ্যতা। গোলাপজাম গাছের নিচের সেই ঘোরের কথা মনে করে এটা বুঝতে পেরেছিলেন গৌতম। আলোকন-প্রত্যাশী নারী-পুরুষ মহাবিশ্বের মৌল কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। জগৎ মারা ও তাঁর সেনাদলের সহিংসতায় শাসিত মনে হলেও প্রেমময় বুদ্ধই অস্তিত্বের মৌল বিধিমালার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মানানসই।
মারার বিরুদ্ধে, আসলে যা নিজের বিরুদ্ধেই, বিজয়ের পর গৌতমকে পিছু টানার মতো আর কিছু ছিল না। দেবতারা স্বর্গ হতে ফিরে এসে তাঁর চূড়ান্ত মুক্তি প্রত্যক্ষ করার জন্যে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছিলেন, কারণ যেকোনও মানুষের মতো তাঁদেরও গৌতমের সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। এবার প্রথম ঝানায় প্রবেশ করলেন গৌতম, তারপর নিজের মনের অন্তস্থ জগতে অনুপ্রবেশ করলেন। অবশেষে নিব্বানার শান্তিতে প্রবেশ করার পর বৌদ্ধবিশ্বের জগৎসমূহ কেঁপে উঠেছিল, স্বর্গ ও নরক আন্দোলিত হয়েছে। বোধিবৃক্ষ আলোকপ্রাপ্ত পুরুষের ওপর লাল ফুল ঝরিয়েছে। গোটা জগৎ জুড়ে,
ফুল গাছ সুশোভিত হয়ে উঠল: ফলজ গাছ নুয়ে পড়ল ফলভারে; গাছে গাছে ফুটল স্থলপদ্ম…দশ হাজার জগতের ব্যবস্থা যেন হাওয়ায় উড়িয়ে দেওয়া ফুলের তোড়ার মতো।[৩৫]
সাগর লোনা স্বাদ হারিয়ে ফেলল। অন্ধ ও মুকরা দেখতে ও শুনতে পেল। পঙ্গুরা ফিরে পেল চলৎশক্তি। কারাগারের বন্দিদের শেকল খসে পড়ল। সহসা সমস্ত কিছু মুক্তি ও সম্ভাবনার দেখা পেল: কয়েক মুহূর্তের জন্যে জীবনের প্রতিটি ধরণ আরও পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।
কিন্তু নতুন বুদ্ধ জগতকে অবতারের মতো করে রক্ষা করতে পারবেন না। প্রতিটি প্রাণীকে নিজ আলোকন লাভের জন্যে গৌতমের কর্মসূচির চর্চা করতে হবে। তিনি তাদের পক্ষে সেটা করে দিতে পারবেন না। কিন্তু গোড়াতে যেন মনে হয়েছে বুদ্ধ, এখন তাঁকে অবশ্যই গৌতম ডাকতে হবে আমাদের, তাঁর সতীর্থ প্রাণীদের রক্ষা করার একমাত্র উপায়, এই ধম্ম প্রচার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। প্রায়শঃই শাক্যমুনি-শাক্য প্রদেশের নীরবজন-অ্যাখ্যায়িত হবেন তিনি, কারণ তাঁর অর্জিত জ্ঞান অনির্বচনীয়, ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তারপরেও গাঙ্গেয় এলাকা জুড়ে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে জনসাধারণ এক নতুন আধ্যাত্মিক দর্শনের আকাঙ্ক্ষা করছিল। পালি টেক্সট আমাদের জানাচ্ছে, প্রায় বুদ্ধ’র আলোকপ্রাপ্তির পরপরই তাপুস্য ও ভালুকা নামে দুজন বণিককে দেবতাদের একজন মহান ঘটনাটি অবহিত করার পর তারা তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে হাজির হলে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল ব্যাপারটা। তারাই প্রথম সাধারণ শিষ্যে পরিণত হয়েছিল।[৩৬] কিন্তু প্রাথমিক সাফল্য সত্ত্বেও অনিচ্ছুক ছিলেন বুদ্ধ। তাঁর ধম্ম ব্যাখ্যা করা বড্ড কঠিন, বলেছেন নিজেকে, লোকে এর জন্যে প্রয়োজনীয় যোগ ও নৈতিক অনুশীলনী চর্চায় আগ্রহী হবে না। আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দেওয়ার বদলে বেশির ভাগ মানুষই ইতিবাচকভাবে তাদের অর্জন উপভোগ করে। আত্ম-পরিত্যাগের বার্তা শুনতে চাইবে না তারা। ‘আমি ধৰ্ম্ম শিক্ষা দিলে,’ সিদ্ধান্ত নেন বুদ্ধ, ‘মানুষ বুঝবে না। আমার জন্যে ক্লান্তিকর ও হতাশাব্যাঞ্জক হয়ে দাঁড়াবে ব্যাপারটা।[৩৭]
কিন্তু দেবতা ব্রহ্মা হস্তক্ষেপ করলেন তখন। নিবিড় মনোযোগের সঙ্গে গৌতমের আলোকপ্রাপ্তি লক্ষ করেছেন তিনি, তাঁর সিদ্ধান্ত জেনে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। বুদ্ধ তাঁর ধম্ম শিক্ষা দিতে অস্বীকৃতি জানালে, হতাশায় চেঁচিয়ে উঠলেন ব্রহ্মা। ‘জগৎ পরাস্ত হবে। কোনও সুযোগই থাকবে না!’ হস্তক্ষেপ করার সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি। পালি টেক্সট সম্পূর্ণ অসচেতনভাবে দেবতাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। দেবতারা তাঁদের সৃষ্টির অংশ। বুদ্ধের কাহিনীতে মারা ও ব্রহ্মার অংশগ্রহণ তুলে ধরা এইসব কিংবদন্তী বুদ্ধমতের নতুন ধর্ম ও প্রাচীন বিশ্বাসের মাঝে সহিষ্ণু অংশীদারী বজায় থাকার বিষয়টিই তুলে ধরে। পৌত্তলিক পড়শিদের প্রতিদ্বন্দ্বী দেবতাদের ভর্ৎসনাকারী হিব্রু পয়গম্বদের বিপরীতে প্রাথমিক বুদ্ধরা বহুসংখ্যক মানুষের প্রথাগত পূজা-অর্চনা বন্ধ করার কোনও প্রয়োজন বোধ করেনি। তার বদলে বুদ্ধ তাঁর জীবনের নির্দিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে দেবতাদের সাহায্য করার সুযোগ করে দিচ্ছেন, এমনটাই দেখিয়েছে। মারার মতো ব্রহ্মাও হয়তো বুদ্ধের ব্যক্তিত্বেরই একটা দিক তুলে ধরে থাকতে পারে। সম্ভবত দেবতারা যে মানুষের অবচেতন শক্তির অভিক্ষেপ, সেটা বোঝানোরই একটা উপায় এটা। ব্রহ্মার হস্তক্ষেপের কাহিনী এমনটা বোঝাতে পারে যে, বুদ্ধের মনে কোনও দ্বিধা ছিল। তাঁর একটা অংশ নিঃসঙ্গতায় ফিরে গিয়ে বিরক্তিহীনভাবে নিব্বানার শান্তি ভোগ করার ইচ্ছে করার সময় আরেকটা অংশ এভাবে সতীর্থ প্রাণীদের স্রেফ অবহেলা করতে পারেন না বলে উপলব্ধি করেছে।
স্বাভাবিক ভূমিকার সম্পূর্ণ উল্টো ভূমিকায় স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্যে নেমে এলেন ব্রহ্মা, নতুন বুদ্ধের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন। ‘প্রভু’ প্রার্থনা জানালেন তিনি, ‘দয়া করে ধম্ম প্রচার করুন…খুব সামান্য আকাঙ্ক্ষা অবশিষ্ট রয়ে গেছে এমন মানুষ এই পদ্ধতির অভাবে আটকা পড়ে আছে। ওদের কেউ কেউ বুঝতে পারে।’ বুদ্ধের কাছে ‘যন্ত্রণায় তলিয়ে যাওয়া মানুষের দিকে তাকাতে’ আবেদন জানালেন তিনি, ‘জগতকে রক্ষা করার জন্যে দূর দূরান্তে সফর করার’[৩৮] আবেদন রাখলেন। সহানুভূতি ছিল বুদ্ধের আলোকনের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। এক কিংবদন্তীতে আছে: গৌতম তাঁর মায়ের হৃদয়ের সমান অবস্থান থেকে একপাশ দিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছেন।[৩৯] এটা আধ্যাত্মিক মানুষের জন্মের একটা উপমা, অবশ্যই আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করার জন্যে নয়। আমরা যখন হৃদয় দিয়ে জীবন যাপন করতে শিখি, ঠিক আমাদের মতোই অন্যের দুঃখ-কষ্ট অনুভব করতে পারি, কেবল তখনই আমরা সত্যিকার অর্থে মানুষ হয়ে উঠি একজন পশুবৎ নারী বা পুরুষ যেখানে নিজের স্বার্থকে সবার আগে স্থান দেয়, আধ্যাত্মিক পুরুষ সেখানে অন্যের দুঃখ-কষ্ট বুঝতে ও দূর করতে শেখে। আমাদের অনেকেই ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের হৃদয়হীন করে রাখি, তরুণ গৌতমের প্রবল প্রতিরক্ষা সম্পন্ন প্রমোদ প্রাসাদের অনুরূপ একটা অবস্থা। কিন্তু বুদ্ধত্ব অর্জনের জন্যে দীর্ঘ ধ্যান ও প্রস্তুতিকালে গৌতম তাঁর সমগ্র সত্তাকে গভীরতম কন্দরে অনুরণিত হতে দিয়েছেন। নিজেকে ‘প্রত্যক্ষ জ্ঞান’-এর সঙ্গে দুঃখ-কষ্টের মহান সত্যকে উপলব্ধি করতে শিখিয়েছেন তিনি, নিজের সাথে একে এক ও সম্পূর্ণ আত্মস্থ না করা পর্যন্ত।আপন নিব্বানায় নিরাপদে বন্দি হয়ে থাকতে পারেননি তিনি। তাহলে এক নতুন ধরনের প্রমোদ প্রাসাদে প্রবেশ করতেন তিনি। এমন প্রত্যাহার ধম্মের আবশ্যকীয় গতিশীলতাকে লণ্ডভণ্ড করত: বুদ্ধ চারটি ‘অপরিমেয়’র অনুশীলন করতে পারেন না, সতীর্থ প্রাণীকূল কুটিল হয়ে ওঠা এক জগতে নিস্তেজ হয়ে পড়ে থাকবে আর বুদ্ধ কেবল আপন আধ্যাত্মিক সুবিধার জন্যে পৃথিবীর চারকোণে দয়াময় অনুভূতি পাঠিয়ে যাবেন, তা হতে পরে না। তিনি যেভাবে সেতো- বিমুক্তি-আলোকনের মুক্তি-অর্জন করেছিলেন তাঁর অন্যতম প্রধান উপায় ছিল প্রেমময়-দয়া ও নিঃস্বার্থ সহানুভূতি। ধম্মের দাবি ছিল তিনি বাজার এলাকায় প্রত্যাবর্তন করবেন, নিজেকে বিষাদপূর্ণ পৃথিবীতে জড়িত করবেন।
দেবতা ব্রহ্মা (কিংবা বুদ্ধের ব্যক্তিত্বের উচ্চতর অংশ) বিরাট সাফল্য হিসাবে এটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। বুদ্ধ সযত্নে তাঁর আবেদন শুনলেন; পালি টেক্সট আমাদের বলছে, ‘বুদ্ধের চোখ দিয়ে সহানুভূতির সঙ্গে পৃথিবীর দিকে তাকলেন তিনি।[৪০] এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য। কেবল আপন মুক্তি অর্জনকারী কেউ বুদ্ধ নন, বরং তিনিই বুদ্ধ যিনি যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে উঠে গেলেও অন্যদের বেদনায় সহানুভূতিশীল হতে পারেন। বুদ্ধ এবার উপলব্ধি করলেন, নিব্বানার পথগুলো সবার জন্যেই ‘হাট করে খোলা’: কীভাবে সতীর্থদের কাছে হৃদয়ের দরজা বন্ধ করবেন তিনি?[৪১] বোধি বৃক্ষের নিচে তাঁর উপলব্ধ সত্যের একটা আবশ্যিক অংশ হচ্ছে অন্যের জন্যে বাঁচাই নৈতিকভাবে বাঁচা। জীবনের পরবর্তী চল্লিশ বছর ক্লান্তিহীনভাবে নগর আর শহরে শহরে ঘুরে দেবতা, পশুপাখি, নারী ও পুরুষের কাছে আপন ধম্ম পৌঁছে দেবেন তিনি। এই প্রেমময় আক্রমণের কোনও সীমাবদ্ধতা থাকবে না।
কিন্তু কে প্রথম শুনবে এই বার্তা? সবার আগে প্রাক্তন গুরু আলারা কালাম ও উদকা রামপুত্তের কথা ভাবলেন বুদ্ধ। কিন্তু কাছেই অপেক্ষামান কয়েকজন দেবতা তাঁকে জানালেন তাঁরা দুজনই সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন। প্রচণ্ড শোকের খবর ছিল এটা। তাঁর গুরুরা ভালো মানুষ ছিলেন। নিশ্চয়ই তাঁরা তাঁর ধম্ম বুঝতে পারতেন। তাঁদের কোনও দোষ না থাকলেও এখন বেদনাময় আরেক জীবনে পতিত হয়েছেন তাঁরা। এই সংবাদ বুদ্ধকে নতুন তাগাদা দিয়ে থাকতে পারে। এরপর সেই পাঁচ ভিক্ষুর কথা ভাবলেন তিনি যারা তাঁর সঙ্গে প্রায়শ্চিত্তমূলক তাপস অনুশীলন করেছিলেন। প্রথম খাদ্য গ্রহণের পর সভয়ে সরে গিয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু ওই প্রত্যাখ্যানকে বিচার-বিবেচনাকে ঘোলা করতে দেবেন না তিনি। এক সঙ্গে অবস্থানের সময় তাঁদের সহায়তা ও সমর্থনের কথা ভাবলেন। সরাসরি বেরিয়ে পড়লেন তাঁদের খোঁজে। তাঁরা এখন বারানসির (আধুনিক বানারস) বাইরে হরিণ বাগিচায় বাস করছেন জানতে পেরে ধম্মের চাকা চালু করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে যাত্রা শুরু করলেন তিনি। তিনি যেভাবে বলেছেন, ‘নিব্বানার মৃত্যুহীন ঢোল বাজানোর জন্যে।’[৪২] খুব বেশি কিছু প্রত্যাশা করেননি তিনি। ভ্রান্তিবশত বুদ্ধ ভেবেছিলেন তাঁর শিক্ষা মাত্র কয়েক শো বছর অনুসৃত হবে। কিন্তু মানুষকে উদ্ধার করতে হবে; এবং বুদ্ধ তাঁর অর্জিত নিব্বানার প্রকৃতির কারণেই তাঁদের জন্যে যথাসাধ্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন।
তথ্যসূত্র
১. জোসেফ ক্যাম্পবেল, অরিয়েন্টাল মিথলজি: দ্য মাস্কস্ অভ গড, নিউ ইয়র্ক, ১৯৬২, ২৩৬।
২. মাজহিমা নিকয়া, ৩৬।
৩. প্রাগুক্ত।
৪. আঙুত্তারা নিকয়া ৯: ৩; মাজহিমা নিকয়া, ৩৮, ৪১।
৫. মাজহিমা নিকয়া ২৭, ৩৮, ৩৯, ১১২।
৬. প্রাগুক্ত, ১০০।
৭. দিঘা নিকয়া, ৩২৭।
৮. সামুত্তা নিকয়া, ২: ৩৬।
৯. বিনয়া: মহাভাগ্য, ১: ৬।
১০. উদনা, ৩: ১গ।
১১. মাজহিমা নিকয়া, ৩৮।
১২. প্রাগুক্ত।
১৩. মাজহিমা নিকয়া, ২।
১৪. হারমান অলদেনবার্গ, দ্য বুদ্ধা: হিজ লাইফ, হিজ ডকট্রিন, হিজ অর্ডার (অনু: উইলিয়াম হোয়ে), লন্ডন, ১৮৮২, ২৯৯-৩০২; এডোয়ার্ড কনযে, বুদ্ধজম: ইটস্ এসেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, অক্সফোর্ড, ১৯৫৭, ১০২।
১৫. আঙুত্তারা নিকয়া, ৮: ৭: ৩; রিচার্ড এফ, গমব্রিচ, হাউ বুদ্ধজম বিগান: দ্য কন্ডিশনড জেনেসিস অভ দ্য আর্লি টিচিংস, লন্ডন ও আটলান্টিক হাইল্যান্ডস, এনজে, ১৯৯৬, ৬০-৬১।
১৬. মাইকেল কারিথার্স, দ্য বুদ্ধা, অক্সফোর্ড ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৩, ৭৫-৭৭।
১৭. আঙুত্তারা নিকয়া ৪: ২০।
১৮. মাজহিমা নিকয়া ১০০।
১৯, প্রাগুক্ত, ৩৬; সামুত্তা নিকয়া ১২: ৬৫।
২০. সামুত্তা নিকয়া ১২: ৬৫।
২১. মাজহিমা নিকয়া ৩৬।
২২. বিনয়া: মহাভাগ্য ১: ৫।
২৩. দিঘা নিকয়া, ১: ১৮২।
২৪. মাজহিমা নিকয়া, ৩৬।
২৫. আঙুত্তারা নিয়া, ১০.৯৫।
২৬. অলদেনবার্গ, দ্য বুদ্ধা, ২৭৯-৮২।
২৭. সুত্তা-নিপাতা, ৫: ৭।
২৮. জাতকা, ১: ৬৮-৭৬; হেনরি ক্লার্ক ওয়ারেন, বুদ্ধজম ইন ট্রান্সলেশন, ক্যাম্ব্রিজ, ম্যাস, ১৯০০, ৭১-৮৩।
২৯. জাতকা, ১: ৭০।
৩০. প্রাগুক্ত, ১: ৭১।
৩১. মির্চা এলিয়াদ, দ্য স্যাক্রেড অ্যান্ড দ্য প্রোফেন: দ্য নেচার অভ রিলিজিয়ন (অনু. উইলিয়াম আর. ট্রাস্ক), নিউ ইয়র্ক ও লন্ডন, ১৯৫৭, ৩৩- ৩৭; ৫২-৫৪; ১৬৯। জোসেফ ক্যাম্পবেল, দ্য হিরো উইদ আ থাউজেন্ড ফেইসেস, প্রিন্সটন, এনজে, ১৯৮৬, সংস্ক. ৪০-৪৬, ৫৬-৫৮; দ্য পাওয়ার অভ মিথ (বিল ময়ার্সের সঙ্গে) নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৮, ১৬০-৬২।
৩২. জাতকা, ১: ৭২।
৩৩. প্রাগুক্ত, ১: ৭৩।
৩৪. প্রাগুক্ত, ১: ৭৪।
৩৫. প্রাগুক্ত, ১: ৭৫।
৩৬. বিনয়া: মাহভাগ্য, ১: ৪।
৩৭. প্রাগুক্ত, ১: ৫।
৩৮. প্রাগুক্ত।
৩৯. এলিয়াদ, স্যাক্রেড অ্যান্ড প্রোফেন, ২০০; ক্যাম্পবেল, দ্য পাওয়ার অভ মিথ, ১৭৪-৭৫।
৪০. বিনয়া: মহাভাগ্য, ১: ৫।
৪১. প্রাগুক্ত।
৪২. প্রাগুক্ত, ১: ৬।
৪. ধম্ম
কিন্তু বুদ্ধের শিক্ষাদানের প্রথম প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। গয়া যাবার পথে উপকা নামের পূর্ব পরিচিত এক জৈনের দেখা পান তিনি। বন্ধুর পরিবর্তন নিমেষে লক্ষ করেছিল সে। ‘তোমাকে দারুণ প্রশান্ত লাগছে! কত সজাগ!’ চেঁচিয়ে বলেছে সে। ‘কী শান্ত তুমি। তোমার চেহারা পরিষ্কার। চোখজোড়া উজ্জ্বল। তোমার গুরু কে? আজকাল কার ধম্ম অনুসরণ করছ?’ নিখুঁত ছিল সুচনাটা। বুদ্ধ জানালেন, তাঁর কোনও গুরু নেই। কোনও সংঘেরও সদস্য নন তিনি। এখন পর্যন্ত জগতে তাঁর মতো আর কেউ নেই, কারণ তিনি আরাহান্ত, ‘সফল জনে’ পরিণত হয়েছেন, যিনি পরম আলোকন লাভ করেছেন। ‘কী?’ অবিশ্বাসের সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল উপকা। “নিশ্চয়ই নিজেকে বুদ্ধ, জিনা, আধ্যাত্মিক বিজয়ী, পবিত্রজন দাবি করছ না, আমরা যাঁর অপেক্ষা করছি?’ ‘হ্যাঁ,’ জবাব দিলেন বুদ্ধ। তিনি সকল আকাঙ্ক্ষা জয় করেছেন। প্রকৃতই তাঁকে জিনা ডাকা যেতে পারে। সংশয়ের চোখে তাঁকে দেখল উপকা। মাথা নাড়ল: ‘বন্ধু, স্বপ্ন দেখে যাও,’ বলল সে। ‘আমি চললাম এই দিকে।’ হঠাৎ মূল রাস্তা ছেড়ে একটা পার্শ্ববর্তী পথ বেছে নিল সে, নিব্বানার প্রত্যক্ষ পথ অস্বীকার করল।[১]
বিচ্যুত না হয়ে ব্রাহ্মণদের শিক্ষার পাদপীঠ ও গুরুত্বপূর্ণ শহর বারানসির উদ্দেশে যাত্রা অব্যাহত রাখলেন বুদ্ধ। অবশ্য শহরে বেশি দিন থাকলেন না তিনি। সরাসরি ইসিপাতানার উপকণ্ঠের হরিণ-বাগিচার দিকে চললেন। যেখানে সাবেক পাঁচ সঙ্গী থাকার কথা জানা ছিল তাঁর। তাঁকে এগিয়ে আসতে দেখে সতর্ক হয়ে উঠলেন ওই ভিক্ষুরা। তাঁরা যতদূর জানতেন, তাঁদের পুরোনো মন্ত্রণাদাতা গৌতম পবিত্রজীবন ত্যাগ করে বিলাসিতা ও আত্ম-তুষ্টির জীবন বেছে নিয়েছেন। তাঁকে আর আগের মতো স্বাগত জানাতে পারলেন ন তাঁরা, একজন মহান সাধুঁকে যেভাবে সম্মান জাননো প্রয়োজন ছিল। কিন্তু অহিংসার প্রতি নিবেদিত ভালো মানুষ ছিলেন তাঁরা। তাঁকে কষ্ট দিতে চাইলেন না। তাঁরা স্থির করলেন, দীর্ঘ যাত্রার শেষে বিশ্রাম নিতে চাইলে গৌতম খানিকটা সময় তাঁদের সঙ্গে বসতে পারেন। কিন্তু বুদ্ধ কাছে আসার পর পুরোপুরি নিরস্ত্র হয়ে পড়লেন তাঁরা। সম্ভবত তাঁরাও তাঁর নতুন প্রশান্তি ও আত্মবিশ্বাস দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন, কারণ ভিক্ষুদের একজন নিজের পোশাক ও বাটি নিয়ে তাঁকে স্বাগত জানাতে ছুটে এসেছিলেন। অন্যরা আসন প্রস্তুত, পানি যোগাড়, পিড়ি আর তোয়ালে আনতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, যেন তাঁদের পুরোনো নেতা পা ধুতে পারেন। তাঁকে ‘বন্ধু’[২] বলে আন্তরিকতার সঙ্গে স্বাগত জানালেন তাঁরা। প্রায়ই ঘটবে এমন। বুদ্ধের আচরণের দয়া ও সহানুভূতি প্রায়শঃ একইভাবে মানুষ, দেবতা ও প্রাণীকূলের মাঝে বৈরিতা দূর করবে।
সোজাসুজি কাজের কথায় চলে এলেন বুদ্ধ। এখন আর তাঁকে বন্ধু ডাকা উচিত হবে না তাদের, ব্যাখ্যা করলেন তিনি, কারণ তাঁর আগের সত্তা অদৃশ্য হয়ে গেছে। সম্পূর্ণ ভিন্ন মর্যাদা পেয়েছেন তিনি। এখন একজন তথাগত তিনি, এক অদ্ভুত পদবী, যার আক্ষরিক অর্থ, ‘এভাবে গত।’ তাঁর অহমবাদ নিৰ্বাপিত হয়েছে। তিনি পবিত্রজীবন পরিত্যাগ করেছেন, এমন যেন তাঁরা না ভাবেন; বরং সম্পূর্ণ উল্টোটাই সত্যি। তাঁর বক্তব্যে আকর্ষণীয় দৃঢ়তা ও তাগিদ ছিল যা সঙ্গীরা আগে কখনও শোনেননি। ‘শোন!’ বললেন তিনি, ‘আমি নিব্বানা মৃত্যুহীন অবস্থা অর্জন করেছি। আমি তোমাদের নির্দেশনা দেব! ধম্ম শিক্ষা দেব!’[৩] তাঁরা তাঁর শিক্ষা শুনলে, অনুশীলন করলে, তাঁরাও আরাহান্তে পরিণত হতে পারবেন, তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে পরম সত্যে প্রবেশ করে নিজেদের জীবনে একে বাস্তবে পরিণত করতে পারবেন। কেবল মনোযোগ দিয়ে তাঁর কথা শুনতে হবে তাঁদের।
এরপর প্রথম হিতপোদেশ দিলেন বুদ্ধ। টেক্সটে তা ধম্মাকাপ্পাবাত্তানা-সুত্তা অর্থাৎ ধম্মের চাকা ঘোরানোর বয়ান নামে রক্ষিত আছে, কারণ তা শিক্ষাকে জগতে প্রকাশ করে মানবজাতির জন্যে এক নতুন যুগ সূচনা করেছে। যারা এখন জীবন যাপনের শুদ্ধ উপায় জানে। নিগূঢ় অধিবিদ্যিক তথ্য প্রদান নয়, বরং পাঁচ ভিক্ষুকে আলোকনের পথ দেখানোই এর উদ্দেশ্য। তাঁরাও তাঁর মতো অরাহান্ত হতে পারবেন, কিন্তু কখনও গুরুর সমকক্ষ হতে পারবেন না, কারণ বুদ্ধ নিজ প্রচেষ্টায় একা এবং কারও সাহায্য ছাড়া নিব্বানা লাভ করেছেন। মানুষ জাতিকে শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে সাম্মা সামবুদ্ধ হয়ে পরম আলোকনের গুরু-আরও উচ্চ মর্যাদা লাভ করেছেন তিনি। পরবর্তীকালের বৌদ্ধ শিক্ষা উল্লেখ করবে যে, প্রতি ৩২,০০০ বছরে একবার, যখন ধম্মের জ্ঞান পৃথিবী হতে সম্পূর্ণ হারিয়ে যাবে, সাম্মা সামবুদ্ধ পৃথিবীতে আগমন করবেন। গৌতম আমাদের কালের বুদ্ধে পরিণত হয়েছিলেন। ইসিপাতানার হরিণ বাগিচায় শুরু করেছিলেন তাঁর ধর্মীয় জীবন।
কিন্তু কী শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন তিনি? মতবাদ বা বিশ্বাসের কোনও অবকাশ ছিল না বুদ্ধের: কোনও ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়ার ছিল না তাঁর, দুঃখের মূল কারণ সম্পর্কে কোনও তত্ত্ব নয়, আদি পাপের কোনও গল্পও নয়; নয় পরম বাস্তবতার কোনও সংজ্ঞা। এই ধরনের আঁচ-অনুমানে কোনও যুক্তি খুঁজে পাননি তিনি। বিশেষ অনুপ্রাণিত ধর্মীয় মতামতকে যারা ধর্ম বিশ্বাসের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে বুদ্ধ মতবাদ তাদের কাছে অস্বস্তিকর। ব্যক্তির ধর্মতত্ত্ব বুদ্ধের কাছে সম্পূর্ণ উপেক্ষার বিষয়! অন্য কারও কথায় কোনও মতবাদ গ্রহণ করা তাঁর চোখে একটা ‘অদক্ষ’ অবস্থা যা আলোকনের দিকে চালিত করতে পারে না, কারণ তা ব্যক্তিগত দায়িত্বের বরখেলাপ। কোনও প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসে আত্মসমর্পণে কোনও কৃতিত্ব দেখেননি তিনি। নিব্বানার অস্থিত্বে আস্থা এবং নিজে তার প্রমাণ করার প্রতিজ্ঞাই ‘বিশ্বাস’। বুদ্ধ সব সময় জোর দিয়ে বলেছেন, শিষ্যরা যেন তাঁর শিক্ষা নিজস্ব অভিজ্ঞতায় যাচাই করে নেয়, কিছুই যেন শোনা কথায় মেনে না নেয়। ধর্মীয় ধারণা অনায়াসে আঁকড়ে থাকার আরেকটা বস্তু মানসিক প্রতিজ্ঞায় পরিণত হতে পারে, অথচ ধম্মের উদ্দেশ্যে মানুষকে বিসর্জনে সহায়তা যোগানো।
‘বিসর্জন দেওয়া’ ছিল বুদ্ধের শিক্ষার অন্যতম মূল সুর। আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি সবচেয়ে কর্তৃত্বপূর্ণ নির্দেশনাও আঁকড়ে থাকে না বা অবলম্বন করে না। সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী। কিছুই টিকে থাকে না। শিষ্যরা তাদের সত্তার প্রতি তন্ত্রীতে এই বিষয়টি শনাক্ত করতে না পারা পর্যন্ত নিব্বানা অর্জন করতে পারবে না। নিজেদের কম্ম সম্পাদনের পর এমনকি খোদ তাঁর শিক্ষাও ত্যাগ করতে হবে। একবার তিনি তাদের ভেলার সঙ্গে তুলনা করেছেন। সুবিশাল জলরশির মুখোমুখি হয়ে সেটা পেরুনোর জন্যে মরিয়া এক পর্যটকের গল্প বলেছেন। কোনও সেতু, ফেরি ছিল না সেখানে, নিজেই ভেলা বানিয়ে নদ। পার হয় সে। কিন্তু তারপর, বুদ্ধ শ্রোতাদের জিজ্ঞেস করলেন, ভেলা দিয়ে পর্যটকের কী করা উচিৎ? ওটা উপকারে এসেছে বলে পিঠে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ হবে তার? যেখানে যাবে সাথে করে নিয়ে যাবে? নাকি স্রেফ বেঁধে রেখে যাত্রা অব্যাহত রাখবে? উত্তরটা পরিষ্কার। ‘ঠিক একইভাবে, ভিক্ষুগণ, আমার শিক্ষা নদী পেরুনোর কাজে লাগানোর জন্যে একটা ভেলার মতো, আঁকড়ে থাকার জন্যে নয়,’ উপসংহার টেনেছেন বুদ্ধ। ‘তোমরা সঠিকভাবে ভেলাসুলভ প্রকৃতি বুঝতে পারলে, এমনকি সুশিক্ষা ও (ধম্ম) ত্যাগ করবে, অশুভগুলোর কথা তো না বললেই চলে।’[৪] তাঁর ধৰ্ম্ম পুরোপুরি প্রায়োগিক ছিল। অনিচনীয় সংজ্ঞা প্রদান বা কোনও শিষ্যের অধিবিদ্যিক প্রশ্নের বুদ্ধিবৃত্তিক কৌতূহল মেটানো এর কাজ ছিল না। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বেদনার নদী পেরিয়ে ‘দূরের পাড়ে’ পৌঁছাতে মানুষকে সক্ষম করে তোলা। তাঁর কাজ ছিল দুঃখ-কষ্ট দূর ও শিষ্যদের নিব্বানা অর্জনে সাহায্য করা। এই লক্ষ্য পূরণ করেনি এমন যেকোনও কিছুই যেকোনও রকম গুরুত্বহীন।
সেকারণেই এখানে মহাবিশ্বের সৃষ্টি বা পরম সত্তার অস্তিত্ব সংক্রান্ত কোনও দুর্বোধ্য তত্ত্ব নেই। এসব বিষয় আগ্রহোদ্দীপক হতে পারে, কিন্তু সেগুলো শিষ্যকে আলোকন এনে দেবে না বা দুঃখ হতে মুক্তি দেবে না। কোসাম্বির সিমসাপা বনে বাস করার সময় বুদ্ধ একদিন কিছু পাতা ছিঁড়ে শিষ্যদের দেখালেন, গাছে আরও পাতা বেড়ে উঠছে। তিনিও তেমনি তাদের সামান্য কিছু শিক্ষা দিয়ে আরও অনেক শিক্ষা তুলে রেখেছেন। কেন? ‘কারণ, শিষ্যগণ, সেগুলো তোমাদের কাজে আসবে না, পবিত্রতার সন্ধানে সেগুলো উপযোগি নয়; ওসব শান্তি ও নিব্বানার প্রত্যক্ষ জ্ঞানে পৌঁছে দেবে না।’[৫] দর্শন নিয়ে বারবার প্রশ্ন করে চলা সন্ন্যাসীদের একজনকে তিনি বলেছেন, সে একজন আহত মানুষের মতো যে কিনা তাকে আঘাতকারী ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা না জানা পর্যন্ত চিকিৎসা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে। অর্থহীন এসব তথ্য পাবার আগেই সে মারা যাবে। ঠিক একইভাবে যার জগৎ বিশ্বজগতের সৃষ্টি বা পরম সম্পর্কিত তথ্য পাওয়ার আগে বুদ্ধের শিক্ষা অনুসরণে অস্বীকৃতি জানায় তারা এইসব দুর্ভেয় তথ্য জানবার আগেই কষ্ট ভোগ করে মারা যাবে। বিশ্বজগৎ সৃষ্ট বা চিরন্তন হয়ে থাকলে কী এসে যাবে? শোক, দুঃখ-কষ্ট ও দুর্দশা তারপরও থাকবে। কেবল বেদনা বিনাশের সঙ্গেই বুদ্ধের সম্পর্ক। ‘আমি বর্তমানে অসুখী অবস্থার প্রতিকারের উপদেশ দিতে এসেছি।’ দার্শনিকভাবে আগ্রহী ভিক্ষুকে বলেছিলেন বুদ্ধ, ‘সুতরাং আমি তোমাদের কাছে কোন কোন বিষয় ব্যাখ্যা করিনি এবং তার কারণ সব সময় মনে রাখবে।’[৬]
কিন্তু হরিণ বাগিচায় পাঁচ সাবেক সঙ্গীর সাথে সাক্ষাতের পর একটা কিছু দিয়ে শুরু করতে হয়েছিল বুদ্ধকে। কীভাবে ওদের সন্দেহ দূর করবেন তিনি? চারটি মহান সত্য সম্পর্কে কোনও ধরনের যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিতে হয়েছিল তাঁকে। আমরা জানি না, সেদিন পাঁচ ভিক্ষুকে আসলে কী বলেছিলেন তিনি। পালি টেক্সটে প্রথম হিতোপদেশ নামের বয়ানটি সেদিনের ধর্মোপদেশের হুবহু বিবরণ হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। ধর্মগ্রন্থসমূহ সংকলিত হওয়ার সময় সম্পাদকগণ সম্ভবত সুবিধাজনকভাবে অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহ চালুকারী এই সুত্তার দেখা পেয়ে এই পর্যায়ে বর্ণনায় সংযোজন করেছেন।’[৭] কিন্তু যেভাবেই হোক, প্রথম হিতোপদেশ যথার্থ ছিল। বুদ্ধ সবসময়ই তাঁর শিক্ষাকে যে জনসাধারণকে তিনি শিক্ষা দিচ্ছেন তাদের উপযোগি করে তোলার বিষয়ে যত্নবান ছিলেন। পাঁচ ভিক্ষু গৌতমের কৃচ্ছ্রতা ত্যাগের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন। সুতরাং বর্তমান সুত্তায় তাঁর মধ্যপন্থার মূল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে তাঁদের আশ্বস্ত করার মাধ্যমে শুরু করেছিলেন। যেসব মানুষ ‘অগ্রযাত্রা’য় নেমে পবিত্র জীবনে গিয়েছে, বলেছেন তিনি, তাদের উচিৎ একদিকে ইন্দ্রিয় সুখের দুটি চরম রূপ এবং অন্যদিকে চরম কৃচ্ছ্রতা সাধন এড়িয়ে যাওয়া। কোনওটাই উপকারী নয়, কারণ এগুলো নিব্বানার দিকে চালিত করে না। তার বদলে তিনি এই দুই বিকল্পের মাঝে এক সুখকর মধ্যপন্থা, অষ্টশীল পথ আবিষ্কার করেছেন, এবং নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারেন সন্ন্যাসীদের তা সরাসরি আলোকনের দিকে নিয়ে যাবে।
এরপর বুদ্ধ চারটি মহান সত্যের রূপরেখা দিলেন: দুঃখ-কষ্টের সত্য, দুঃখ-কষ্টের কারণের সত্য, দুঃখ-কষ্ট অবসান বা নিব্বানার সত্য এবং এই মুক্তি অভিমুখী পথের সত্যি। অবশ্য এই সত্যগুলোকে অধিবিদ্যিক তত্ত্ব নয় বরং প্রায়োগিক কর্মসূচি হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ধম্ম শব্দটি কেবল কী নয়, বরং কী হওয়া উচিৎ তাও বোঝায়। বুদ্ধ’র ধম্ম ছিল জীবনের সমস্যা- সংকটের রোগ নির্ণয় ও প্রতিষেধকের ব্যবস্থাপত্রও, যা হুবহু অনুসরণ করতে হবে। তাঁর হিতোপদেশে প্রতিটি সত্যের তিনটি উপাদান ছিল। প্রথমে তিনি ভিক্ষুদের সত্য প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। এরপর এ ব্যাপারে কী করতে হবে সেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন: দুঃখ-কষ্টকে ‘সম্পূর্ণভাবে’ জানতে হবে,’ দুঃখ-কষ্টের কারণ ‘আকাঙ্ক্ষা’ ‘বিসর্জন দিতে হবে’: দুঃখ-কষ্টের অবসান, নিব্বানাকে আরাহান্তের হৃদয়ে একটি ‘বাস্তবতায়’ পরিণত হতে হবে। এবং অষ্টশীল পথ ‘অবশ্যই’ অনুসরণ করতে হবে। সবশেষে, তিনি স্বয়ং কী অর্জন করেছেন তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন বুদ্ধ: তিনি ‘প্রত্যক্ষভাবে দুঃখকে উপলব্ধি করেছেন: আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করেছেন: নিব্বানার অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন: শেষ পর্যন্ত তিনি এর পথ অনুসরণ করেছেন। এটা, ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি, যখন নিজের কাছে ধম্মের কার্যকারিতা প্রমাণ করেছেন ও বাস্তব অর্থে কর্মসূচি সম্পাদন করেছে, তখনই আলোকন সম্পূর্ণ হয়েছে: ‘চূড়ান্ত মুক্তি অর্জন করেছি আমি।’ বিজয়ীর সুরে চিৎকার করেছে তিনি।[৮] সত্যিই সামসারা হতে মুক্ত হয়েছিলেন তিনি। জানতেন মধ্যপন্থাই সত্যি পথ। নিজ জীবন ও ব্যক্তিত্ব সেটা প্রমাণ করেছে।
পালি টেক্সট আমাদের বলছে, বুদ্ধের হিতোপদেশ শোনার সময় পাঁচ ভিক্ষুর অন্যতম কোন্দান্না ‘প্রত্যক্ষভাবে’ তাঁর শিক্ষা অনুভব করতে শুরু করেছিলেন। যেন সত্তার গভীরতা থেকে তাঁর মাঝে ‘জেগে উঠেছিল’ এটা। যেন চিনতে পেরেছিলেন তিনি-বরাবরই জানা ছিল।[১০] এভাবেই সবসময় ধর্মগ্রন্থগুলো কোনও নতুন শিষ্যের ধম্মে শিক্ষা গ্রহণের বর্ণনা দিয়েছে। এটা বিশ্বাসের প্রতি কোনও ধারণাগত সম্মতি ছিল না। আসলে হরিণ বাগিচায় দীক্ষানুষ্ঠান সম্পাদন করেছিলেন বুদ্ধ। ধাত্রীর মতো একজন আলোকপ্রাপ্ত মানুষের জন্মে সহায়তা দান করছিলেন, বা তাঁর নিজস্ব উপমা ব্যবহার করে বলা যায়, খাপ হতে তরবারি বা খোলস হতে সাপ বের করে আনছিলেন তিনি। প্রথম হিতোপদেশ শোনার জন্যে হরিণ বাগিচায় সমবেত দেবতাগণ কোন্দান্নার পরিবর্তন লক্ষ করে আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন: ‘প্রভু বারানসির হরিণ বনে ধম্মের চাকা চালু করেছেন!’ দেবতাদের চিৎকার একের পর এক আকাশে অন্য দেবতাদের কাছে পৌঁছে গেল। শেষে খোদ ব্রহ্মার কানেও গেল। ধরণী কেঁপে উঠল, দেবতার চেয়েও উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠল ‘কোন্দান্না জানে! কোন্দান্না জানে!’ খুশিতে চেঁচালেন বুদ্ধ। বৌদ্ধ ট্র্যাডেশন অনুযায়ী ‘স্রোতে প্রবেশকারীতে’ (সোতাপান্না)[১১] পরিণত হয়েছিলেন কোন্দান্না। পুরোপুরি আলোকপ্রাপ্ত হননি বটে, কিন্তু তাঁর সন্দেহ কেটে গিয়েছিল। তিনি আর অন্য কোনও ধম্মে আগ্রহী ছিলেন না। বুদ্ধের পদ্ধতিতে অবগাহন করতে প্রস্তুত ছিলেন তিনি; জানতেন এটাই তাঁকে নিব্বানার দিকে নিয়ে যাবে। বুদ্ধের সংঘে যোগদানের আবেদন জানালেন তিনি। ‘এসো, ভিক্ষু,’ জবাব দিলেন বুদ্ধ। ‘ধম্ম চমৎকারভাবেই প্রচার করা হয়েছে। পবিত্র জীবন যাপন করো, যা তোমার দুঃখ কষ্টকে চিরকালের জন্যে দূর করে দেবে।[১২]
কিন্তু পালি টেক্সট হরিণ বনের এই প্রথম শিক্ষার আরেকটি ভাষ্য অন্তর্ভুক্ত করেছে। এটা আরও দীর্ঘ এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রক্রিয়ার বর্ণনা দেয়। জোড়ায় জোড়ায় ভিক্ষুদের নির্দেশনা দিয়েছেন বুদ্ধ, অন্যদিকে বাকি তিনজন ওদের ছয়জনের জন্যে পর্যাপ্ত খাদ্য যোগাড় করতে বারানসিতে চলে গেছেন। এখানে বোঝানো হয়েছে, অধিকতর নিবিড় এই শিক্ষায় ভিক্ষুদের তাঁর বিশেষ যোগ শিক্ষা দিচ্ছিলেন বুদ্ধ, ‘অভিনিবেশ’ ও ‘অপরিমেয়’র সাথে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।[১৩] ধ্যান অবশ্যই আলোকনের জন্যে অপরিহার্য। শিক্ষাব্রতীরা বুদ্ধের যোগীয় অনুবীক্ষণের নিচে দেহ-মন স্থাপন করতে না শিখলে ও নিজেদের গভীরে ডুব না দিলে ধম্ম ‘প্রত্যক্ষভাবে’ উপলব্ধি করা যাবে না বা বাস্তবতায় পরিণত হবে না। কেবল হিতোপদেশ শুনে আর লোকমুখে শোনা সত্যসমূহ গ্রহণ করে কোন্দান্না ‘স্রোতে প্রবেশকারী’ হয়ে তাঁর ‘প্রত্যক্ষ জ্ঞান’ অর্জন করতে পারবেন না। ভিক্ষুরা আপন অভিজ্ঞতার পরতে পরতে দুঃখ-কষ্ট ও আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে সজাগ না হওয়া পর্যন্ত সঠিকভাবে তাঁর সত্য অনুধাবন করা যাবে না। তাঁর শিক্ষার অষ্টশীল পথে ধ্যানের অনুশীলনও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পাঁচ ভিক্ষুকে দেওয়া নির্দেশনা প্রায় নিশ্চিতভাবেই একটি মাত্র সকালের চেয়ে বেশি সময় নিয়েছিল। আগে হতেই তাঁরা সফল যোগি ও অহিংসা নীতিতে দক্ষ হয়ে থাকলেও ধম্মের কার্যকর হতে সময় প্রয়োজন ছিল। যাই হোক, পালি টেক্সট আমাদের বলছে, কোন্দান্নার মাঝে ধম্ম ‘জেগে ওঠার’ অল্প পরেই বাপ্পা, বাদ্যিয়, মহানামা ও আশাজিও ‘স্রোতে প্রবেশকারী’তে পরিণত হন।[১৪]
ধম্মের যৌক্তিক গঠন ধ্যানের অনুশীলনের পরিপূরক ছিল যা শিক্ষার্থীকে তা ‘উপলব্ধি’ করতে সক্ষম করে তুলত। যোগের মাধ্যমে ভিক্ষুগণ মতবাদ কোন্ সত্যি ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছে তা শনাক্ত করতে পারতেন। বৌদ্ধদের ধ্যানের অন্যতম প্রধান বিষয় হচ্ছে নির্ভরশীল ঘটনার ধারা (পাতিক্কাসমুপদ), যা বুদ্ধ সম্ভবত পরবর্তী কোনও পর্যায়ে দুঃখ-কষ্টের সত্যের সম্পূরক হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। যদিও পালি টেক্সটগুলো আলোকপ্রাপ্তির অব্যবহিত আগে-পরেই এই ধারা বিবেচনা করেছেন বরে উল্লেখ করেছে।[১৫] এই ধারা বারটি শর্তাধীন ও নিয়ন্ত্রণের সম্পর্কের মাধ্যমে আমাদের জীবনের ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতি তুলে ধরে চেতনাশীল কোনও সত্তার জীবন চক্রের সন্ধান করে এবং দেখায় কীভাবে প্রতিটি মানুষ চিরন্তনভাবে ভিন্ন কিছুতে পরিণত হচ্ছে।
[১] অজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে [২] কম্ম: কম্মের উপর নির্ভর করে [৩] চেতনাঃ চেতনার উপর নির্ভর করে [৪] নাম ও ধরণ: নাম ও ধরনের উপর নির্ভর করে [৫] ইন্দ্রিয় অঙ্গ: ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে [৬] সংযোগ: সংযোগের উপর নির্ভর করে [৭] অনুভূতি: অনুভূতির উপর নির্ভর করে [৮] আকাঙ্ক্ষা: আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভর করে [৯] সম্পর্ক: সম্পর্কের উপর নির্ভর করে [১০] অস্তিত্ব: অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে [১১] জন্ম: জন্মের উপর নির্ভর করে [১২] দুঃখ: বয়স ও মৃত্যু, দুঃখ, বিলাপ, দুর্দশা, শোক ও হতাশা।[১৬]
এই ধারাক্রম বৌদ্ধ শিক্ষার কেন্দ্রিয় বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এটা উপলব্ধি করা সহজ নয়। এটা যাঁদের কাছে নিরুৎসাহব্যঞ্জক ঠেকে, তাঁরা এই ভেবে আশ্বস্ত হতে পারেন যে, বুদ্ধ একবার এক ভিক্ষুকে এটা সহজ মনে করায় ভর্ৎসনা করেছিলেন। একে উপমা হিসাব দেখতে হবে, এক জীবন হতে অন্য জীবনে টিকে থাকার মতো কোনও সত্তা না থাকা সত্ত্বেও–যেমনটা বুদ্ধ উপলব্ধি করছিলেন–মানুষ কেমন করে পুনর্জন্ম লাভ করতে পারে এটা যখন সেটাই বোঝানোর চেষ্টা করে। কী সেই জিনিস যা আবার জন্ম নেয়? এমন কোনও আইন আছে যা পুনর্জন্মকে দুঃখের সঙ্গে সম্পর্কিত করে?
ধারায় ব্যবহৃত পরিভাষাগুলো কিঞ্চিৎ দুর্বোধ্য। যেমন ধরা যাক ‘নাম ও ধরণ’ স্রেফ পালি বাকধারায় ‘ব্যক্তি’; ‘চেতনা’ (বিন্নানা) কোনও ব্যক্তির চিন্তা ও অনুভূতির সামগ্রিকতা নয়, বরং এক ধরনের উচ্চমার্গীয় বস্তু, মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের শেষ ভাবনা বা আবেগ যা তার জীবনের সকল কম্ম দিয়ে গঠিত হয়েছে। এই ‘চেতনা’ মায়ের জঠরে এক নতুন ‘নাম ও ধরনের’ বীজানুতে পরিণত হয়। ভ্রুণের ব্যক্তিত্ব পূর্বসুরির মৃত্যুপথযাত্রী ‘চেতনা’র শর্তাধীন। এই ‘চেতনা’র সঙ্গে যখন ভ্রূণ সম্পর্কিত হয়, তখনই নতুন এক জীবনচক্র সূচিত হতে পারে। ভ্রূণ ইন্দ্রিয় অঙ্গগুলোর বিকাশ ঘটায়। জন্মের পর এগুলো বাহ্যিক জগতের সঙ্গে ‘যোগাযোগ’ করে। এই ইন্দ্রিয়জ সম্পর্ক ‘শিহরণ’ বা অনুভূতির জন্ম দেয় যা দুঃখের সবচেয়ে শক্তিশালী কারণ ‘আকাঙ্ক্ষা’র দিকে চালিত করে। আকাঙ্ক্ষা চালিত করে ‘সম্পর্কের’ দিকে যা আমাদের মুক্তি ও আলোকন প্রতিহত করে। আমাদের যা নতুন ‘অস্তিত্বে’ নতুন জন্ম ও আরও দুঃখ, অসুস্থতা, শোক আর মৃত্যুতে ঠেলে দেয়।[১৭]
অজ্ঞতা দিয়ে সূচিত হয় এই ধারা যা দুঃখকষ্টের সবচেয়ে শক্তিশালী না হলেও প্রধান কারণে পরিণত হয়। গাঙ্গেয় অঞ্চলের অধিকাংশ সন্ন্যাসী আকাঙ্ক্ষাই দুঃখের প্রথম কারণ বলে বিশ্বাস করতেন। এদিকে উপনিষদ ও সমক্ষ্যের ধারণা ছিল যে বাস্তবতার প্রকৃতি সম্পর্কে অজ্ঞতাই মুক্তির পথে প্রধান অন্তরায়। বুদ্ধ এ দুটো কারণকে সম্পর্কিত করতে পেরেছিলেন।[১৮] তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রতিটি মানুষ বেঁচে আছে, কেননা চারটি কারণ সম্পর্কে অজ্ঞ সত্তার মাধ্যমে সে সাবেক অস্তিত্বে বিরাজ করেছে। ফলে নিজেদের তারা আকাঙ্ক্ষা ও ভোগান্তির কবল হতে মুক্ত করতে পারে না। সঠিকভাবে ওয়াকিবহাল নয় এমন মানুষ মারাত্মক বাস্তব ভুল করতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, একজন যোগি ভাবতে পারে যে ঘোরের কোনও একটি উচ্চতর পর্যায়ই নিব্বানা। ফলে সম্পূর্ণ মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে সে আর বাড়তি প্রয়াস পাবে না। পালি টেক্সটে দেওয়া ধারাক্রমের অধিকাংশ ভাষ্যে দ্বিতীয় ধারাটি কম্ম নয় নয়, বরং আরও কঠিন বিষয় সাংখারা (গঠন)। কিন্তু দুটো শব্দই একই ক্রিয়াপদ মূল হতে নেওয়া: ক্র (করা)। সাংখারা শব্দটিকে কিছুটা দুর্বোধ্যভাবে অনুবাদ করা হয়েছে: ‘অবস্থা বা বস্তু যা গঠন বা প্রস্তুত হচ্ছে।’[১৯] এভাবে আমাদের কর্মকাণ্ড (কম্ম) আগামী অস্থিত্বের ‘চেতনা’ গঠন করছে: তাকে আকার নিচ্ছে ও শর্তাধীন করছে। বুদ্ধ যেহেতু আমাদের ইচ্ছাগুলোকে মানসিক কৰ্ম্ম হিসাবে দেখেছেন, ধারাক্রম দেখাচ্ছে যে, আমাদের বাহ্যিক কর্মকাণ্ডকে প্ররোচিতকারী আবেগসমূহের ভবিষ্যৎ পরিণাম থাকবে: লোভী, বিভ্রান্ত পছন্দের একটি জীবন আমাদের শেষ, মৃত্যুপযাত্রী চিন্তার (বিন্নানা) মানকে প্রভাবিত করবে। এটা আবার পরবর্তীকালে আমরা কোন জীবন পাব তাকে প্রভাবিত করবে। নতুন ‘নাম ও ধরনে’ বাহিত এই শেষ, মৃত্যুপথযাত্রী ‘চেতনা’ কী চিরন্তন, স্থির অস্তি ত্ব? একজন ব্যক্তি কী বারবার জীবন যাপন করবে? হ্যাঁ এবং না। চেতনাকে যোগিদের মতো স্থায়ী, চিরন্তন সত্তা বলে বিশ্বাস করতেন না বুদ্ধ। একে বরং এক সলতে থেকে আরেক সলতেয় যাওয়া শিখার মতো অন্তিম টিমটিমে শক্তি হিসাবে দেখেছেন।[২০] অগ্নিশিখা কখনওই ধ্রুব নয়। সন্ধ্যারাতে জ্বালানো আগুনই ভোরবেলার জ্বলন্ত আগুন, আবার ঠিক তা নয়।
ধারাক্রমে কোনও স্থির সত্তা নেই। প্রতিটি কাড়া অন্যটির ওপর নির্ভরশীল ও সরাসরি ভিন্ন কিছুর দিকে চালিত করে। এটা মানুষের জীবনের অনিবার্য সত্য হিসাবে বুদ্ধের দেখা ‘হয়ে ওঠার’ এক নিখুঁত প্রকাশ। আমরা সব সময়ই ভিন্ন কিছু হতে চাই। এক নতুন ধরনের সত্তার জন্যে যুদ্ধ করছি। সত্যিকার অর্থেই দীর্ঘদিন একই অবস্থায় থাকতে পারি না। প্রতিটি সাংখারা পরবর্তীটিকে জায়গা ছেড়ে দেয়: প্রতিটি অবস্থা স্রেফ অন্যটির ভূমিকা। সুতরাং, জীবনের কোনও কিছুকেই স্থিতিশীল হিসাবে দেখা যাবে না। ব্যক্তিকে একটি প্রক্রিয়া হিসাবে দেখাতে হবে, অপরিবর্তনীয় কোনও সত্তা নয়। একজন ভিক্ষু ধারাক্রম নিয়ে ধ্যান করার সময় যোগির দৃষ্টিতে একে দেখতে পান, প্রতিটি শিহরণের উত্থান-পতনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে মনোযোগি হয়ে ওঠেন, তখন কোনও কিছুর উপর ভরসা করা যাবে না, সমস্ত কিছুই অস্থায়ী (অনিক্ক), এই সত্যের ‘প্রত্যক্ষ জ্ঞান’ অর্জন করেন তিনি। তিনি তখন কার্য ও কারণের এই অন্তহীন ধারাক্রম হতে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে দ্বিগুণ প্রয়াস চালাবেন।[২১]
অবিরাম আত্মমূল্যায়ন ও দৈনন্দিন জীবনের উত্থান-পতনের দিকে মনোযোগ এক ধরনের শীতল নিয়ন্ত্রণ এনে দেয়। ধ্যানে অভিনিবেশের দৈনিক অনুশীলন অব্যাহত থাকলে তা ভিক্ষুকে আরও গভীরে প্রোথিত ব্যক্তিত্ব ও যৌক্তিক বিশ্লেষণে উপস্থাপযোগ্য ব্যক্তিত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি এনে দেয়। ব্রাহ্মণদের কৃচ্ছতার ঘোরের জন্যে অবকাশ ছিল না বুদ্ধের। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, তাঁর ভিক্ষুদের সংযমের সঙ্গে চলতে হবে এবং আবেগ প্রকাশ হতে বিরত থাকতে হবে। কিন্তু অভিনিবেশ ভিক্ষুকে তাঁর আচরণের নৈতিকতা সম্পর্কে আরও সজাগ করে তোলে। তিনি তখন তার ‘অদক্ষ’ কর্মকাণ্ড কেমন করে অন্যদের ক্ষতি সাধন করতে পারে এবং তাঁর অনুপ্রেরণাও কেমন করে ক্ষতিকারক হতে পারে সেটা লক্ষ করেন। তো, বুদ্ধ উপসংহার টেনেছেন, আমাদের ইচ্ছা কম্ম এবং তার পরিণাম রয়েছে।[২২] অচেতন বা সচেতন ইচ্ছা, যা আমাদের কর্মকাণ্ডকে উৎসাহ যোগায় সেগুলো মানসিক কাজ যা যে কোনও বাহ্যিক কাজকর্মের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। চেতনা হিসাবে (ইচ্ছা : পছন্দ) কম্মের পুনঃসংজ্ঞা ছিল বিপ্লবাত্মক। নৈতিকতার সামগ্রিক প্রশ্নকে তা গভীর করে তুলেছে। যা কিনা এখন মনে আর হৃদয়ে স্থাপিত, বাহ্যিক আচরণের কোনও ব্যাপার হতে পারবে না।
কিন্তু অভিনিবেশ (সাতি) বুদ্ধকে আরও ভিন্নতর উপসংহারে চালিত করেছে। পাঁচ জন ভিক্ষুর ‘স্রোতে প্রবেশকারী’ হবার তিনদিন পর হরিণ বনে দ্বিতীয় হিতোপদেশ দেন বুদ্ধ। এখানে তিনি তাঁর অনাত্মা (সত্তাহীনতা) সম্পর্কিত অনন্য মতবাদের ব্যাখ্যা দেন তিনি।[২৩] মানবীয় ব্যক্তিত্বকে তিনি পাঁচটি ‘স্তূপ’ বা ‘উপাদানে’ (খণ্ড): ভাগ করেন তিনিঃ দেহ, অনুভব, ধারণা, আচরণ (স্বোচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত) ও সচেতনতা। ভিক্ষুদের প্রতিটি খণ্ডের বিষয় ভিন্নভাবে বিবেচনা করার পরামর্শ দেন। যেমন ধরা যাক আমাদের দেহ বা অনুভূতি প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে। এতে করে আমাদের বেদনা যোগাচ্ছে। আমাদের তা হতাশ করে তুলছে। আমাদের আচরণ ও ধারণা সম্পর্কেও একই কথা বলা যায়। প্রতিটি খণ্ড দুঃখের শিকার বলে ত্রুটিপূর্ণ ও ক্ষণস্থায়ী। এর পক্ষে অসংখ্য ভাববাদী ও যোগীদের কাঙ্ক্ষিত সেই সত্তার অনুসন্ধান বা ধরে রাখার ক্ষমতা রাখে না। এটা কি সত্যি নয়, শিষ্যদের জিজ্ঞেস করলেন বুদ্ধ, প্রতিটি খণ্ড পরখ করার পর একজন সৎ ব্যক্তি নিজেকে এর সাথে পুরোপুরি একাত্ম করতে পারছে না বলে আবিষ্কার করবে, কারণ এটা বড় বেশি অসন্তে াষজনক? সে বলতে বাধ্য হবে: ‘এটা আমার নয়, আমি আসলে যা এটা তা নয়: এটা আমার সত্তা নয়।[২৪] কিন্তু বুদ্ধ স্রেফ চিরন্তন, পরম অস্তিত্বের কথা অস্বীকার করেননি। এবার তিনি ঘোষণা করলেন, সিথিশীল নিম্নস্তরের সত্তা বলেও কিছু নেই। ধারা যেমন দেখায়, প্রতিটি সচেতন সত্তা এক অবিরাম পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে: পুরুষ বা নারী স্রেফ ক্ষণস্থায়ী পরিবর্তনশীল অস্তিত্বের ধারাক্রমমাত্র।
বুদ্ধ তাঁর গোটা জীবন এই বার্তাই প্রচার করে গেছেন। সপ্তদশ শতকের ফরাসি দার্শনিক দেকার্তে যেখানে ঘোষণা দেবেন, ‘আমি ভাবি তাই আমি অস্তিত্বশীল’, সেখানে বুদ্ধ সম্পূর্ণ বিপরীত উপসংহারে পৌঁছেছিলেন। নিজের আবিষ্কৃত অভিনিবেশের যোগী পদ্ধতিতে তিনি যত ভেবেছেন ততই পরিষ্কার হয়ে গেছে যে আমরা যাকে ‘সত্তা’ বলি তা আসলে একটা বিভ্রম। তাঁর দৃষ্টিতে, আমরা যত ঘনিষ্ঠভাবে আমাদের যাচাই করব ততই স্থায়ী সত্তা হিসাবে কোনও কিছুকে চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে উঠবে। মানুষের ব্যক্তিত্ব এমন স্থবির অস্তিত্ব নয় যেখানে ঘটনা সংঘটিত হয়। যোগীর অনুবীক্ষণসুলভ বিশ্লেষণের অধীনে স্থাপন করা হলে প্রতিটি ব্যক্তিই একটি প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে। ব্যক্তিত্বের বর্ণনা দেওয়ার বেলায় জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড বা খরস্রোতা ঝর্নার উপমা দিতে পছন্দ করতেন বুদ্ধ। এর এক ধরনের পরিচয় থাকলেও কোও দুটি বিশেষ মুহূর্তে এক নয়। প্রতিটি সেকেন্ডে আগুন ভিন্ন কিছু, নিভে গিয়ে আবার নিজেকে সৃষ্টি করেছে–ঠিক মানুষের মতো। দরাজ হেসে মানুষের মনকে বনেবাদারে ছুটে বেড়ানো বানরের সঙ্গে তুলনা করেছেন বুদ্ধ: ‘একটা ডাল আঁকড়ে ধরে, পরক্ষণে ওটা ছেড়ে আরেকটা ধরে।’[২৫] আমরা যাকে ‘সত্তা হিসাবে অনুভব করি তা আসলে স্রেফ সুবিধাজনক পরিভাষা, কারণ আমরা অবিরত বদলে যাচ্ছি। একইভাবে দুধ পর্যায়ক্রমে দই, মাখন, ঘি এবং ঘিয়ের সূক্ষ্ম নির্যাসে পরিণত হতে পারে। এইসব পরিবর্তনের কোনওটাকে ‘দুধ’ বলার কোনও যুক্তি নেই, যদিও সেটা বললে ঠিক হওয়ার একটা ভাব থাকে। [২৬]
অষ্টাদশ শতকের স্কটিশ অভিজ্ঞতাবাদী ডেভিড হিউম গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যসহ একই ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন: তিনি চাননি তাঁর দর্শন পাঠকদের নৈতিক আচরণকে প্রভাবিত করুক। কিন্তু অ্যাক্সিয়াল যুগের ভারতে রূপান্তরকারী না হলে জ্ঞানের কোনও তাৎপর্য ছিল না। ধম্ম ছিল কাজের আদেশব্যঞ্জক এবং অনাত্মার মতবাদ কোনও বিমূর্ত দার্শনিক প্রস্তাবনা ছিল না, বরং বৌদ্ধদের এমন আচরণ দাবি করত যেন অহমের কোনও অস্তিত্ব নেই। এর নৈতিক প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী, ‘সত্তা’র ধারণাই কেবল ‘আমি ও আমার’ সম্পর্কিত অদক্ষ চিন্তাভাবনা সৃষ্টি ও স্বার্থপর আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তোলে না; অহমবাদকে তর্কসাপেক্ষে সকল অশুভের উৎস হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে; সত্তার সাথে অতিরিক্ত সংযোগ ঈর্ষা বা শত্রুর প্রতি ঘৃণা, প্রতারণা, হামবড়া ভাব, অহঙ্কার, নিষ্ঠুরতা এবং সত্তা আক্রান্ত বোধ করলে, সহিংসতা ও অন্যদের বিনাশ ডেকে আনতে পারে। পশ্চিমাবাসীরা প্রায়শঃই বুদ্ধের অনাত্মার মতবাদকে নাস্তিবাদী ও হতাশাব্যাঞ্জক মনে করে, কিন্তু সর্বোত্তম অবস্থায় অ্যাক্সিয়াল যুগে সৃষ্ট সবগুলো মহান বিশ্বধর্ম দরুণ ক্ষতিকারক সর্বগ্রাসী ভীতকারী আহমকে দমন করতে চেয়েছে। বুদ্ধ অবশ্য আরও বেশি অগ্রসর ছিলেন। তাঁর অনাত্মার মতবাদ সত্তাকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়নি। তিনি স্রেফ সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার গেছেন। একে স্থায়ী বাস্তবতা হিসাবে কল্পনা করা ভুল ছিল। এ জাতীয় যেকোনও ভ্রান্ত ধারণা আমাদের দুঃখ-কষ্টের চক্রের সঙ্গে আটকে রাখা সেই অজ্ঞতারই লক্ষণ।
যেকোনও বৌদ্ধ শিক্ষার মতোই অনাত্মা কোনও দার্শনিক মতবাদ ছিল না, মূলত তা ছিল বাস্তব ভিত্তিক। যোগ ও অভিনিবেশের মাধ্যমে একজন শিষ্য অনাত্মার ‘প্রত্যক্ষ’ জ্ঞান অর্জন করতে পারলে অহমবাদের বেদনা ও বিপদ হতে নিষ্কৃতি পাবে সে, তখন তা যৌক্তিক অসম্ভাব্যতায় পরিণত হবে। অ্যাক্সিয়াল দেশগুলোয় আমরা দেখেছি, স্বর্গ হতে নির্বাসিত এবং জীবনকে অর্থ ও মূল্য প্রদানকারী পবিত্র মাত্রা হতে বঞ্চিত মানুষ সহসা নিঃসঙ্গ, দিশাহারা বোধ করেছে। এক নতুন বাজার অর্থনীতিতে চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জগতে নিরাপত্তাহীনতা হতেই তাদের অধিকাংশ বেদনার সৃষ্টি হয়েছিল। বুদ্ধ তাঁর ভিক্ষুদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, অন্যদের ক্ষতি সাধন করে দাপানো, তোষামোদ করা, ও ফাঁপিয়ে তুলে বাঁচানোর মতো তাদের কোনও ‘সত্তা’ নেই। সন্ন্যাসী অভিনিবেশের অনুশীলনে অভ্যস্থ হয়ে গেলে বুঝতে পারবে, আমরা যাকে ‘সত্তা’ বলি সেটা কত ক্ষণস্থায়ী। তখন আর এইসব চলমান মানসিক অবস্থায় নিজের অহমকে মেলাবে না সে, সেগুলোর সঙ্গে একাত্ম হবে না। নিজের আকাঙ্ক্ষা, ভয় ও কামনাগুলোকে তার সঙ্গে সম্পর্কহীন দূরবর্তী ঘটনা হিসাবে দেখতে শিখবে। একবার এই পক্ষপাতহীনতা ও প্রশান্তি অর্জন করার পর, দ্বিতীয় হিতোপদেশ শেষে পঞ্চভিক্ষুর কাছে ব্যাখ্যা দিলেন বুদ্ধ, নিজেকে আলোকনের উপযোগি হয়ে উঠতে দেখবে সে। ‘তার লোভ মিলিয়ে যাচ্ছে, বাসনা অদৃশ্য হয়ে যাবার পর হৃদয়ের মুক্তি অনুভব করে সে।’ লক্ষ্য অর্জন করেছে সে, আলোকপ্রাপ্ত হওয়ার পর বুদ্ধ যেমন করেছিলেন তেমনি বিজয় উল্লাস প্রকাশ করতে পারে সে। ‘অবশেষে পবিত্র জীবন যাপন করা হয়েছে। যা করার ছিল, সম্পাদন করা হয়েছে; আর কিছুই করণীয় নেই।’[২৭]
এবং প্রকৃতপক্ষে পঞ্চ ভিক্ষু বুদ্ধের অনাত্মার ব্যাখ্যা শোনার পর পাঁচজনই পরিপূর্ণ আলোকপ্রাপ্ত হয়ে আরাহান্তে পরিণত হলেন। টেক্সট আমাদের বলছে, তাঁর শিক্ষা তাঁদের হৃদয়কে আনন্দে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে।[২৮] অদ্ভুত মনে হতে পারে: আমরা যে সত্তার স্বপ্ন দেখি সেটা অস্তিত্বহীন জেনে কেন এত খুশি হবেন তাঁরা? বুদ্ধ জানতেন অনাত্মা ভীতিকর হতে পারে। বহিরাগত কেউ প্রথমবারের মতো এই মতবাদ শুনে ‘আমি নিশ্চিহ্ন, ধ্বংস হয়ে যাব, আমার আর অস্তিত্ব থাকবে না,’[২৯] ভেবে শঙ্কিত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু পালি টেক্সট দেখায়, লোকে পাঁচ ভিক্ষুর মতো ব্যাপক স্বস্তি ও আনন্দের সাথে অনাত্মাকে গ্রহণ করেছে। এতে ‘প্রমাণ’ হয়েছে, এটা সত্যি। মানুষ যখন অহমের অস্তিত্ব নেই ভেবে জীবন যাপন করে, তখন তারা আবিষ্কার করে, তারা আগের চেয়ে খুশি। আমাদের একান্ত মহাবিশ্ব হতে সত্তাকে আসনচ্যুত করে সেখানে অন্যান্য সত্তাকে স্থাপন করার লক্ষ্যে পরিকল্পিত ‘অপরিমেয়’র অনুশীলনের অনুরূপ সত্তার বিস্তৃতি অনুভব করেছে তারা। অহমবাদ সংকীর্ণকারী। আমরা স্বার্থপর দৃষ্টি কোণে দেখার সময় আমাদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ থাকে। আমাদের মর্যাদা ও বেঁচে থাকার তীব্র উদ্বেগ হতে সৃষ্ট লোভ, ঘৃণা ও নাগালের বাইরের যাপিত জীবন কাঠামো মুক্তি নির্দেশক। বিমূর্ত ধারণা হিসাবে উত্থাপিত হলে অনাত্মাকে অনুজ্জ্বল মনে হতে পারে, কিন্তু অভিজ্ঞতায় নেওয়া হলে মানুষের জীবন পাল্টে দেয়। যেন অহমের অস্তিত্ব নেই, এমনিভাবে জীবন যাপন করে মানুষ অহমবাদকে জয় করেছে বলে আবিষ্কার করেছে এবং অনেক ভালো বোধ করেছে। একজন যোগির ‘প্রত্যক্ষ জ্ঞান’ দিয়ে অনাত্মাকে উপলব্ধি করে তারা এক সমৃদ্ধ, পূর্ণ অস্তি ত্বে পৌঁছেছে। সুতরাং অনাত্মা নিশ্চয়ই আমাদের মানবীয় অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানায়। যদিও সত্তার অস্তিত্ব না থাকার বিষয়টি আমরা হাতে কলমে প্রমাণ করতে পারব না।
বুদ্ধ বিশ্বাস করতেন, স্বার্থহীন জীবন নারী ও পুরুষকে নিব্বানার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবে। একেশ্বরবাদীরা বলবে, এটা তাদের ঈশ্বরের সত্তায় পৌঁছে দেবে। কিন্তু একজন ব্যক্তিরূপ উপাস্যের ধারণাকে খুবই সীমাবদ্ধ মনে করেছেন বুদ্ধ, কারণ এটা বোঝায়, পরম সত্তা স্রেফ আরেকটা সত্তা মাত্র। নিব্বানা কোনও ব্যক্তি বা স্বর্গের মতো কোনও জায়গা নয়। বুদ্ধ সব সময় কোনও পরম নিয়ম বা মহা সত্তার অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন, কেননা সেটা আঁকড়ে থাকার আরেকটা বস্তু, আরেকটা শৃঙ্খল, আলোকনের পথে আরেকটা বিঘ্ন হয়ে উঠতে পারে। সত্তার মতবাদের মতো ঈশ্বরের ধারণাও অহমকে উস্কে দেওয়া ও ফাঁপিয়ে তোলার কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। ইহুদি, ক্রিশ্চান ও ইসলামের সবচেয়ে স্পর্শকাতর একেশ্বরবাদীগণ এই বিপদ সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠবে ও ঈশ্বর প্রসঙ্গে এমনভাবে কথা বলবে যা নিব্বানা সম্পর্কে বুদ্ধের সংযমের স্মারক। তারা জোর দিয়ে একথাও বলব যে, ঈশ্বর স্রেফ আরেকটা সত্তা মাত্র নন; ‘সত্তা’ সম্পর্কে আমাদের ধারণা এত সীমিত যে ঈশ্বর অস্তি ত্বহীন, অর্থাৎ ‘তিনি’ আসলে কিছু না বলাটাই অনেক সঠিক। কিন্তু অধিকতর জনপ্রিয় স্তরে এটা নিশ্চিতভাবে সত্যি যে, ‘ঈশ্বর’কে প্রায়শঃই ‘তাঁর’ উপাসকদের কল্পনা ও পছন্দ মাফিক প্রতিমায় পরিণত করা হয়। ঈশ্বরকে আমরা আমাদেরই মতো পছন্দ-অপছন্দ সম্পন্ন করলে ‘তাঁকে’ দিয়ে আমাদের সবচেয়ে সংকীর্ণ, স্বার্থপর ও এমনকি ভীষণ আশা, শঙ্কা আর কুসংস্কারকে মেনে নিতে বাধ্য করা খুবই সহজ হয়ে যায়। এই সীমাবদ্ধ ঈশ্বরের এভাবে ইতিহাসের বেশ কিছু জঘন্য ধর্মীয় নিপীড়নে অবদান রেখেছেন। বুদ্ধ আমাদের নিজস্ব সত্তায় পবিত্র অনুমোদনের সীলমোহর দানকারী উপাস্যে বিশ্বাসকে ‘অদক্ষ’ বর্ণনা করতেন; এটা কেবল বিশ্বাসীকে ক্ষতিকর ও বিপজ্জনক অহমবাদেই বন্দি করে রাখবে, যেটা তার ছাড়িয়ে যাবার কথা। আলোকন দাবি করে, আমরা তেমন কোনও মেকি জাঁক প্রত্যাখ্যান করব। মনে হয় ‘অনাত্মার’ প্রত্যক্ষ যোগ উপলব্ধি অন্যতম প্রধান উপায় যার মাধ্যমে আদি বৌদ্ধরা নিব্বানা প্রত্যক্ষ করেছিল। এবং সত্যি সত্যিই অ্যাক্সিয়াল যুগের ধর্মবিশ্বাসগুলো কোনও না কোনওভাবে জোর দিয়েছে যে, কেবল সম্পূর্ণ আত্মপরিত্যাগ অনুশীলন করেই আমরা নিজেদের সম্পূর্ণ করে তুলতে পারব। পরকালে আয়েসী অবকাশ লাভের মতো কোনও কিছুর ‘সন্ধানে’ ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ স্রেফ আসল উদ্দেশ্য ছাড়িয়ে যাওয়া। হরিণ বাগিচায় আলোকনপ্রাপ্ত পাঁচ ভিক্ষু গভীরতর স্তরে এবিষয়টি বুঝতে পেরেছিলেন।
এবার অন্যদের কাছে ধম্ম পৌঁছে দিতে হবে তাঁদের। স্বয়ং বুদ্ধ যেমন উপলব্ধি করেছিলেন, দুঃখের প্রথম মহান সত্যি উপলব্ধির মানে অন্যের দুঃখ- কষ্টে সহানুভূতিশীল হওয়া; অনাত্মার মতবাদ বোঝায়, একজন আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিজের জন্যে নয় বরং অন্যদের জন্যে বেঁচে থাকবে। এখন আরাহান্তের সংখ্যা ছয় জন, কিন্তু বেদনায় আবৃত বিশ্বে আলোক পৌঁছে দেওয়ার জন্যে সংখ্যাটা খুবই কম। তারপর যেন জাদুমন্ত্র বলে বুদ্ধের ছোট সংঘে নতুন সদস্যের জোয়ার দেখা দিল। প্রথমজন ছিলেন বারানসির এক ধনী বণিকের ছেলে ইয়াসা। তরুণ গৌতমের মতো বিলাসিতায় জীবন কাটাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু একরাতে ঘুম থেকে জেগে দেখেন খাটের চারপাশে ঘুমাচ্ছে তাঁর ভৃত্যরা, ওদের এমন কুৎসিত, বিশ্রী ভঙ্গি দেখে বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠেন তিনি। নাদান কথার মতো অন্যান্য টেক্সট কোনও রকম দুঃখ প্রকাশ ছাড়াই তরুণ গৌতম সম্পর্কে একই কাহিনী বলার ব্যাপারটি কাহিনীর আদি আদর্শ প্রকৃতি তুলে ধরে। গাঙ্গেয় অঞ্চলে অসংখ্য মানুষের অনুভূত বিচ্ছিন্নতাকেই বর্ণনা করেছেন ইয়াসা। পালি টেক্সট আমাদের বলছে, অন্তর থেকে বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠা ইয়াসা যন্ত্রণায় চিৎকার করে বললেন, ‘এ যে ভয়ঙ্কর! মারাত্মক।’ সহসা জগৎ অশ্লীল, অর্থহীন মনে হলো, অসহনীয়ও বটে। অবিলম্বে ভালো কিছুর সন্ধানে ‘সামনে বাড়ার’ সিদ্ধান্ত নিলেন ইয়াসা। একজোড়া সোনার চপ্পল পায়ে গলিয়ে পা টিপেটিপে বাবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে বিড়বিড় করে ‘ভয়ঙ্কর! মারাত্মক! বলতে বলতে হরিণ বাগিচার উদ্দেশে রওনা হলেন। বুদ্ধের সামনে পড়ে গেলেন তারপর। ভোরে ঘুম থেকে উঠে শীতল আলোয় হাঁটছিলেন তিনি আলোকপ্রাপ্ত মানুষের বর্ধিত মানসিক শক্তিতে ইয়াসাকে চিনতে পারলেন বুদ্ধ। ইশারায় তাঁকে বসতে বলে হাসি মুখে বললেন: ‘এটা ভয়ঙ্কর নয়। মারাত্মক নয়। এসো, বসো, ইয়াসা। তোমাকে ধম্ম শিক্ষা দেব আমি।’[৩০]
বুদ্ধের প্রশান্তি ও কোমলতা মুহূর্তে স্বস্তি যোগাল ইয়াসার। সেই অসুস্থকর আতঙ্ক রইল না তাঁর, নিজেকে বরং সুখী ও আশাবাদী বোধ করতে লাগলেন। মন আনন্দময় ও শান্ত থাকায় আলোকনের জন্যে সবচেয়ে উপযোগি অবস্থায় ছিলেন তিনি। চপ্পল খুলে বুদ্ধের পাশে বসে পড়লেন তিনি। তাঁকে মধ্যপন্থার শিক্ষা দিলেন বুদ্ধ। ধাপে ধাপে তানহা ও ইন্দ্রিয়জ সুখ এড়ানোর মৌল শিক্ষার মাধ্যমে শুরু করলেন, পবিত্র জীবনের সুবিধার বর্ণনা দিলেন। যখন দেখলেন ইয়াসা মনোযোগি ও প্রস্তুত, তাঁকে চারটি মহান সত্যি শিক্ষা দিতে শুরু করলেন তিনি। শোনার সময় ‘ধম্মের খাঁটি দৃশ্য জেগে উঠল’ ইয়াসার মাঝে, এমনভাবে তাঁর আত্মায় তলিয়ে গেল যেমন করে, আমাদের যেভাবে বলা হয়েছে, রঙ কাপড়ে ভেতরে প্রবেশ করে তাকে রাঙিয়ে তোলে।[৩১] ইয়াসার মন ধম্মে ‘রঞ্জিত’ হবার পর দুটোকে আর আলাদা করার উপায় ছিল না। এটাই ‘প্রত্যক্ষ জ্ঞান,’ কারণ ইয়াসা এমন গভীর স্তরে ধম্ম অনুভব করেছেন যে তিনি এর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। এটা তাঁর সম্পূর্ণ সত্তাকে ‘রঞ্জিত’ করেছে। লোকে প্রথম ধম্মের কথা শোনার সময়, বিশেষ করে খোদ বুদ্ধ দীক্ষা দেওয়ার সময় এটাও সাধারণ অভিজ্ঞতায় পরিণত হবে। ধম্ম তাঁদের প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খেয়ে যাচ্ছে ভেবেছে তারা, এটা তাদের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও অনুকূল; এক অর্থে আগাগোড়াই জানা ছিল তাদের। পালি টেক্সটে আমরা দামাস্কাসের পথে সেইন্ট পলের যন্ত্রণাকর বা নাটকীয় ধর্মান্তরের মতো কোনও ঘটনার উল্লেখ দেখি না। এ ধরনের যেকোনও হৃদয়বিদারক অভিজ্ঞতাকে বুদ্ধ ‘অদক্ষ’ বিবেচনা করতেন। মানুষকে অবশ্যই তার স্বভাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে, যেমনটি গোলাপজাম গাছের নিচে ছিলেন তিনি।
ইয়াসা ‘স্রোতে প্রবেশকারী’ হওয়ার পরই বুদ্ধ লক্ষ করলেন আরেক প্রবীন বণিক এগিয়ে আসছেন ওঁদের দিকে। তিনি বুঝে গেলেন, নিশ্চয়ই ইয়াসার বাবা হবেন। তখন অধিকতর দক্ষতায় প্রাপ্ত বিবেচিত ইদ্ধি বা আধ্যাত্মিক ক্ষমতা বলে ইয়াসাকে অদৃশ্য করে দিলেন তিনি। দারুণ বিচলিত ছিলেন ইয়াসার বাবা। তাঁর গোটা বাড়ি ইয়াসার খোঁজে ব্যস্ত, কিন্তু তিনি সোনার চপ্পলের ছাপ অনুসরণ করেছেন, যা তাঁকে সরাসরি বুদ্ধের কাছে নিয়ে এসেছে। আবার বণিককে বসালেন বুদ্ধ। আভাসে জানালেন অচিরেই ইয়াসাকে দেখতে পাবেন তিনি। ছেলের মতো একইভাবে নির্দেশনা দিলেন বাবাকে। নিমেষে মুগ্ধ হয়ে গেলেন বণিক: ‘প্রভু, এ অনন্য! সত্যি অনন্য!’ চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি। ‘ধৰ্ম্ম এমন স্পষ্ট করা হয়েছে যেন আপনি অন্ধকারে লণ্ঠন ধরে রেখে ভুল হয়ে যাওয়া একটা কিছু শুদ্ধ করে দিচ্ছেন।’ এরপর প্রথমবারের মতো তিনি বুদ্ধ, ধম্ম ও ভিক্ষুদের সংঘের প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা প্রকাশকারী ঘোষণা ত্রি-আশ্রয় নামে নামে পরিচিত হয়ে ওঠা আচার পালন করলেন।[৩২] প্রথম সাধারণ অনুসারীদের প্রথম ব্যক্তিতে পরিণত হলেন তিনি, যিনি সংসারী থেকেও বৌদ্ধদের পদ্ধতির এক পরিবর্তিত ধরণ অনুসরণ করেছেন।
বাবার চোখের আড়ালে বুদ্ধে কথা শোনার সময় সম্পূর্ণ আলোকপ্রাপ্ত হলেন ইয়াসা, প্রবেশ করলেন নিব্বানায়। এই পর্যায়ে বুদ্ধ তাঁকে তাঁর বাবার সামনে প্রকাশ করলেন। ইয়াসাকে কেবল তাঁর মায়ের জন্যে হলেও বাড়ি ফিরে যেতে অনুনয় করলেন বণিক। অবশ্য বুদ্ধ ধীরে ধীরে তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন, ইয়াসা একজন আরাহাস্তে পরিণত হয়েছেন। তাঁর পক্ষে এখন গৃহস্থের জীবন যাপন অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। এখন আর গৃহস্থের প্রজনন ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে তোলার মতো বাসনা ও আকাঙ্ক্ষায় আক্রান্ত নন তিনি। ধ্যানের জন্যে এখন তাঁর দীর্ঘ নীরবতা ও নিরিবিলি পরিবেশ প্রয়োজন হবে, সংসারী জীবনে যা সম্ভব হবে না। ফিরে যেতে পারবেন না তিনি। বুঝতে পারলেন ইয়াসার বাবা। কিন্তু বুদ্ধকে সেদিন তাঁর বাড়িতে আহার গ্রহণের আবেদন জানালেন। ইয়াসা হবেন তাঁর পরিচারক সন্ন্যাসী। খাবারের সময় ইয়াসার মা ও প্রাক্তন স্ত্রীকে দীক্ষা দিলেন বুদ্ধ। তারাও বুদ্ধের প্রথম মহিলা সাধারণ অনুসারীতে পরিণত হয়।
কিন্তু এ খবর পরিবারের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ল। বারানসির নেতৃস্থানীয় চার বণিক পরিবারের সদস্য ইয়াসার পার বন্ধু তাঁর গেরুয়া বসন পরার খবরে এতটাই বিমোহিত হয়ে গিয়েছিলেন যে দীক্ষা নিতে বুদ্ধের কাছে হাজির হলেন তারা। আশপাশের পল্লী এলাকা হতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরিবারের ইয়াসার পঞ্চাশ জন বন্ধুও তাই করলেন। অভিজাত ও বনেদী গোত্রের এইসব তরুণ অচিরেই আলোকপ্রাপ্ত হলেন। ফলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই, টেক্সটসমূহ আমাদের বলছে, খোদ বুদ্ধসহ পৃথিবীতে আরাহান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল একষট্টি জনে।
উল্লেখযোগ্য গোত্রে পরিণত হচ্ছিল সংঘ। কিন্তু নতুন আরাহান্তদের সদ্যপ্রাপ্ত মুক্তি নিয়ে বিলাসিতা করতে দেওয়া চলবে না। তাদের বৃত্তি জগৎ হতে স্বার্থপর পশ্চাদপসরণ নয়, অন্যদের বেদনা হতে মুক্তি অর্জনে সাহায্য করার জন্যে বাজার এলাকায় প্রত্যাবর্তন করতে হয়েছিল তাঁদের। এখন ধম্মের নির্দেশ মোতাবেক অন্যদের জন্যে বাঁচাবেন তারা। ‘এবার যাও,’ ষাটজন ভিক্ষুকে বললেন বুদ্ধ।
জগতের জন্যে সহানুভূতি দেখিয়ে দেবতা আর মানুষের সুবিধা, কল্যাণ ও সুখের জন্যে ভ্রমণ করো। দুজন একই পথে যেয়ো না। ধম্ম শিক্ষা দাও, ভিক্ষুগণ, পবিত্র জীবন নিয়ে ধ্যান কর। অন্তরে সামান্য আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ধৰ্ম্ম না শোনায় কষ্ট ভোগ করছে কিছু সত্তা। তারা এটা বুঝতে পারবে।[৩৩]
বুদ্ধ মতবাদ সুবিধাপ্রাপ্ত অভিজাত গোষ্ঠীর মতবাদ ছিল না। ‘সাধারণ মানুষের ‘অনেকের’ (বহুজনা) ধর্ম ছিল। বাস্তব ক্ষেত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উচ্চবিত্ত ও বুদ্ধিজীবীদের কাছে আবেদন রাখলেও তাত্ত্বিকভাবে সবার জন্যে খোলা ছিল এটা এবং ধর্ম-বর্ণ যাই হোক না কেন কারও জন্যে এর দরজা রুদ্ধ ছিল না। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কেউ একজন এমন এক ধর্মীয় কর্মসূচির স্বপ্ন দেখেছেন যা একক কোনও দলের মাঝে সীমিত ছিল না, বরং সমগ্র মানব জাতির জন্যেই চিন্তা করা হয়েছে। উপনিষদের সাধুদের প্রচারিত মতবাদের মতো এটা কোনও নিগূঢ় পথ ছিল না, বাজার এলাকায়, নব প্রতিষ্ঠিত শহরে, বাণিজ্য পথ বরাবর সবার জন্যে উন্মুক্ত ছিল। মানুষ যখনই ধৰ্ম্মের কথা শুনেছে, গাঙ্গেয় অঞ্চলে বিবেচনা করার মতো একটি শক্তিতে পরিণত হওয়া সংঘে এসে ভিড় করেছে তারা। নতুন ব্যবস্থায় সদস্যরা ‘শাক্য গুরুর নির্দেশপ্রাপ্ত অনুসারী’ নামে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু নিজেদের তারা স্রেফ ভিক্ষুদের সংঘ (ভিক্ষু-সংঘ) হিসাবে আখ্যায়িত করতেন।[৩৪] যোগদানকারী লোকেরা এতদিন সুপ্ত থাকা মানবতার সমগ্র এলাকায় ‘জাগ্রত’ হয়েছে বলে আবিষ্কার করেছে। এক নতুন সামাজিক ও ধর্মীয় বাস্তবতা অস্তিত্ব লাভ করেছিল।
তথ্যসূত্র
১. বিনয়া: মহাভাগ্য, ১: ৬।
২. প্রাগুক্ত।
৩. প্রাগুক্ত।
৪. মাজহিমা নিকয়া, ২২।
৫. সামুত্তা নিকয়া ৫৩: ৩১।
৬. মাজহিমা নিকয়া, ৬: ৩।
৭. বিনয়া: মহাভাগ্য, ১: ৬; সাম্যত্তা নিকয়া, ৫৬: ১১।
৮. প্রাগুক্ত।
৯. পরবর্তী কালের বৌদ্ধ ধারাভাষ্য অনুযায়ী শিশু গৌতমকে পরখ করতে আগত ব্রাহ্মণ ছিলেন কোন্দান্না। গৌতম বুদ্ধ হবেন বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেন তিনি। দীক্ষার অভিজ্ঞতা থাকায় তিনি সবসময় অন্নাতা কোন্দান্না: সবজান্তা কোন্দান্না নামে পরিচিত ছিলেন।
১০. বিনয়া: মহাভাগ্য, ১: ৬।
১১. প্রাগুক্ত।
১২. প্রাগুক্ত। আমাদের জানানো হয়েছে যে, আদি এই বৌদ্ধরা ‘স্রোতে প্রবেশকারী’ হতে মাত্র সাতটি আগামীজীবন নিয়ে পরিপূর্ণ আলোকিত মানুষ আরাহান্তে উন্নীত হয়ে সামসারা হতে সম্পূর্ণ মুক্তি অর্জন করেছেন। পরবর্তী কাহিনী শিক্ষা দিয়েছে যে, অধিকাংশ মানুষের জন্যে দুটো মধ্য পার্যায়ের পথ রয়েছে: [১] ‘প্রত্যাবর্তনীয়’ (সাকাদাগামী), যার কেবল একটি প্রত্যবর্তন অবশিষ্ট রয়েছে; [২] ‘অপ্রত্যাবর্তনীয়’ (অনাগামী), যিনি কেবল স্বর্গে দেবতা হিসাবে জন্ম নেবেন।
১৩. মাজহিমা নিকয়া, ২৬, টিলমেন ভেতার, দ্য আইডিয়াজ অ্যান্ড মেডিটেটিভ প্র্যাকটিসেস অভ আর্লি বুদ্ধজম, লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, কোপেনহাগেন ও কোলন, ১৯৮৬, xxix।
১৪. বিনয়া: মহাভাগ্য, ১: ৬।
১৫. সাম্যত্তা নিকয়া, ১২: ৬৫; দিঘা নিকয়া, ১৪; বিনয়া: মহাভাগ্য, ১: ১; উদনা, ১: ১-৩।
১৬. বিনয়া: মহাভাগ্য, ১: ১।
১৭. মাইকেল কারিথার্স, দ্য বুদ্ধা, অক্সফোর্ড ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৩, ৬৮- ৭০; হারমান অলদেনবার্গ, দ্য বুদ্ধা, হিজ লাইফ, হিজ ডকট্রিন, হিজ অর্ডার (অনু. উইলিয়াম হোয়ে), লন্ডন, ১৮৮২, ২২৪-৫২; কার্ল জেস্পারস, দ্য গ্রেট ফিলোসফার্স: দ্য ফাউন্ডেশনস (অনু. রালফ্ মেইনহেইম), লন্ডন, ১৯৬২, ৩৯- ৪০; ভেতার, আইডিয়াজ অ্যান্ড মেডিটেটিভ প্র্যাকটিসেস, ২৪০-৪২।
১৮. রিচার্ড এফ. গমব্রিচ, থেরাভেদা বুদ্ধজম: আ সোশ্যাল হিস্ট্রি ফ্রম অ্যানশেন্ট বেনারেস টু মডার্ন কলোম্বো, লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৮, ৬২-৬৩; অলদেনবার্গ, দ্য বুদ্ধা, ২৪০-৪২; কারিথার্স, দ্য বুদ্ধা, ৬৬।
১৯. ভেতার, আইডিয়াজ অ্যান্ড মেডিটেটিভ প্র্যাকটিসেস, ৫০-৫২; অলদেনবার্গ, দ্য বুদ্ধা, ২৪৩-৪৭।
২০. ভেতার, আইডিয়াজ অ্যান্ড মেডিটেটিভ প্র্যাকটিসেস, ৪৯-৫০।
২১. অলদেনবার্গ, দ্য বুদ্ধা, ২৪৮-৫১; কারিথার্স, দ্য বুদ্ধা, ৫৭-৫৮।
২২. আঙুত্তারা নিকয়া ৬: ৬৩।
২৩. বিনয়া: মহাভাগ্য, ১: ৬; সাম্যত্তা নিকয়া, ২২: ৫৯।
২৪. প্রাগুক্ত।
২৫. সাম্যত্তা নিকয়া, ২২: ৬১।
২৬. দিঘা নিকয়া, ৯।
২৭. বিনয়া: মহাভাগ্য, ১: ৬।
২৮. প্রাগুক্ত।
২৯. মাজহিমা নিকয়া ১।
৩০. বিনয়া: মহাভাগ্য ১: ৭।
৩১. প্রাগুক্ত।
৩২. প্রাগুক্ত, ১: ৮, আসলে পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করেন, বুদ্ধের জীবদ্দশায় ভিক্ষুগণ কেবল বুদ্ধের কাছেই ‘একক শরণ’ নিয়েছেন। বুদ্ধের মৃত্যুর আগে ‘ত্রি-শরণ’ বাধ্যতামূলক হয়নি।
৩৩. বিনয়া: মহাভাগ্য ১: ১১।
৩৪. সুকুমার দত্ত, বুড্ডিস্ট মক্কস অ্যান্ড মনাস্টারিজ অভ ইন্ডিয়া, লন্ডন, ১৯৬২, ৩৩।
৫. ব্ৰত
বৌদ্ধ শিল্পকর্মসমূহ সাধারণত দেখায় যে, বুদ্ধ নিঃসঙ্গ ধ্যানমগ্ন অবস্থায় একাকী বসে আছেন। কিন্তু বাস্তবে ধম্ম প্রচার শুরু করার পর থেকে তাঁর জীবনের সিংহভাগ সময়ই কেটে গেছে বিশাল কোলাহলময় জনতার ভীড়ে। ভ্রমণের সময় সাধারণত শত শত ভিক্ষু সঙ্গী হতেন তাঁর। তাঁরা এত জোরে কথাবার্তা বলতে চাইতেন যে অনেক সময় নীরব থাকার জন্যে আবেদন জানাতে বাধ্য হতেন বুদ্ধ। তাঁর সাধারণ অনুসারীরা প্রায়শঃই রথ ও ঠেলাগাড়ি ভর্তি রসদপত্র নিয়ে রাস্তার সন্ন্যাসীদের মিছিল অনুসরণ করত। প্রত্যন্ত বনের কুড়ে ঘরে নয়, শহর ও নগরে বাস করতেন বুদ্ধ। কিন্তু জীবনের শেষ পঁয়তাল্লিশটি বছর সাধারণ মানুষের চোখের সামনে কেটে গেলেও টেক্সটসমূহ এই দীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়টিকে কিছুটা উপেক্ষাই করেছে। জীবনাকারের কাজে লাগার মতো তেমন কিছু রাখেনি। জেসাসের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি একেবারেই উল্টো। গস্পেলসমূহ জেসাসের প্রথম জীবন সম্পর্কে আমাদের প্রায় কিছুই জানায় না, বরং মিশন শুরু করার পরই গুরুত্বের সঙ্গে তাঁর কাহিনী বলা শুরু করেছে। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থসমূহ বুদ্ধের হিতোপদেশসমূহ সংরক্ষণ করেছে এবং তাঁর দীক্ষা প্রদানের প্রথম পাঁচটি বছরের মোটামুটি বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে। অথচ এরপরই দৃষ্টি হতে হারিয়ে যান বুদ্ধ। তাঁর জীবনের শেষ বিশটি বছর প্রায় সম্পূর্ণই অসংকলিত রয়ে গেছে।
এই ধরনের সংযম হয়তো সমর্থন করতেন বুদ্ধ। আর যাই হোক ব্যক্তিকেন্দ্রিক কাল্ট আশা করেননি তিনি, সব সময়ই জোর দিয়ে বলেছেন, তিনি নন, ধম্মই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যেমন উল্লেখ করেছি, তিনি বলতেন, ‘যে আমাকে দেখতে পায় সে ধম্মকেই দেখে।’[১] এছাড়াও, আলোপ্রাপ্তির পর বাস্ত বিক আর কিছু ঘটতে পারত না তাঁর। কোনও ‘সত্তা’ ছিল না তাঁর, অহমবাদ নির্বাপিত হয়েছে; ‘তথাগত’ নামে পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন তিনি, অর্থাৎ যিনি স্রেফ ‘বিদায়’ নিয়েছেন। এমনকি পালি টেক্সটসমূহ তাঁর মিশনের গোড়ার দিকের বছরগুলোর বর্ণনা দেওয়ার সময়ও ঐতিহাসিক তথ্যের চেয়ে বরং তাদের গল্পের প্রতীকী অর্থের প্রতিই বেশি আগ্রহী। আধ্যাত্মিক জীবনের আদর্শ, ধম্ম ও নিব্বানার মূর্ত প্রতাঁকে পরিণত হয়েছিলেন বুদ্ধ। নতুন ধরনের মানুষ ছিলেন তিনি; লোভ ও ঘৃণার নিপীড়নে আবদ্ধ নন। অহমবাদ হতে মুক্ত হয়ে বাঁচার জন্যে নিজের মনকে পরিচালিত করতে শিখেছিলেন তিনি। এই পৃথিবীতেই বাস করলেও ভিন্ন এক মাত্রায় ছিল তাঁর আবাস, একেশ্বরবাদীরা যাকে স্বর্গীয় উপস্থিতি বলবে। সুতরাং, দীক্ষা দানের গোড়ার দিকের বছরগুলোর বর্ণনায় পালি টেক্সটগুলো বুদ্ধের চিন্তা ও অনুভূতি সম্পর্কে আমাদের কিছুই বলে না, কিন্তু উত্তর ভারতের শহর, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি ও ধর্মীয় জগতের সঙ্গে আদি বৌদ্ধদের সম্পর্ক দেখতে তাঁর কর্মকাণ্ডকে ব্যবহার করে।
ধর্মগ্রন্থসমূহ বলে, এপ্রিলের শেষে বা মে-র প্রথম দিকে নিব্বানা লাভ করেন বুদ্ধ। কিন্তু এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কোন বছর ঘটেছিল সেটা প্রকাশ করে না। দীর্ঘদিন ধরে ৫২৮ বিসিইকেই প্রচলিত সন হিসাবে বিবেচনা করা হয়ে আসছিল, যদিও কোনও কোনও আধুনিক পণ্ডিত একে ৪৫০-এর শেষ দিকের ঘটনা মনে করেন।[২] আমরা পালি টেক্সটের সম্ভাব্য ত্বরান্বিত ঘটনাক্রমপঞ্জী অনুসরণ করলে বুদ্ধ সম্ভবত বর্ষা ঋতুর শেষে, সেপ্টেম্বরে ষাট জন সন্ন্যাসীকে দীক্ষা দানের উদেশ্যে প্রেরণ করে থাকবেন। অন্যান্য সংঘের মতো বুদ্ধের নতুন সংগঠনও শিথিল ও ভ্রমণশীল সংস্থা ছিল। যেখানে পারতেন কোনওমতে ঘুমিয়ে থাকতেন সন্ন্যাসীরা: ‘জঙ্গল, গাছপালার নিচে, ঝুলন্ত পাথরের নিচে, গিরিখাতে, পাহাড়ী গুহায়, শ্মাশানে, বনে, প্রকাশ্য স্থানে, খড়ের গাদায়।’[৩] কিন্তু প্রতিদিন ধ্যানে সময় কাটাতেন তাঁরা আর যাদের প্রয়োজন সেইসব মানুষকে, বিশেষ করে সময়ের অস্থিরতা সবচেয়ে তীব্রভাবে অনুভূত হওয়া নতুন শহরগুলোর বাসিন্দাদের ধম্ম দীক্ষা দিতেন। তাঁদের শিক্ষা সফল হয়েছিল: কেবল সাধারণ অনুসারীই সংগ্রহ করেননি তাঁরা বরং সংঘের নতুন সদস্যও পেয়েছিলেন। ষাট সন্ন্যাসীকে নতুন নবীশ সংগ্রহ করে পূর্ণাঙ্গ সন্ন্যাসী হিসাবে দীক্ষা দেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছিলেন বুদ্ধ।[৪]
আরও একবার একাকী হওয়ার পর উরুবেলায় ফিরে এলেন বুদ্ধ। চলার পথে স্থানীয় এক বারবনিতার পিছু ধাওয়াকারী তিরিশজন উচ্ছৃঙ্খল তরুণকে ধম্ম দীক্ষা দেন তিনি। মেয়েটি ওদের টাকা নিয়ে সটকে পড়েছিল। ‘তোমাদের জন্যে কোনটা ভালো?’ জিজ্ঞেস করেন বুদ্ধ, ‘একজন নারীর সন্ধান করা, নাকি নিজেদের খুঁজে পাওয়া?’[৫] ঘটনাটি মানুষের আনন্দের পেছনে অর্থহীন ছুটোছুটি করার একটা স্পষ্ট উপমা, যা কেবল হতাশ ও নিঃস্ব করে তুলতে পারে।
বুদ্ধের কথা শোনার পর তরুণদের সবাইই ‘স্রোতে প্রবেশকারীতে পরিণত হয়ে সংঘে যোগ দেয়। কিন্তু উরুবেলায় পৌঁছার পর উরুবেলা, গয়া ও নিরঞ্জরা নদীর পাশের বনে সাফল্যের সঙ্গে তিন কশ্যপ ভাইদের নেতৃত্বে বসবাসকারী হাজার সদস্যের গোটা একটা সংঘকে দীক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে আরও চমকপ্ৰদ ধর্মান্তর অর্জন করেন তিনি। কাহিনীটিকে সম্ভবত বৈদিক ট্র্যাডিশনের সঙ্গে আদি বৌদ্ধদের মোকাবিলা তুলে ধরা উদাহরণ হিসাবে পড়া উচিত।[৬] এই ব্রাহ্মণরা ‘অগ্রসর হয়েছেন’ ও সাধারণ সমাজের স্থির, শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবনধারা প্রত্যাখ্যানের প্রতীক হিসাবে চুল বড় হতে দিয়ে জট পাকাতে দিয়েছেন। কিন্তু তখনও তাঁরা প্রাচীন আচার-অনুষ্ঠান পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করতেন। তিনটি পবিত্র অগ্নিকুণ্ডের যত্ন নিচ্ছিলেন তাঁরা।
পুরো শীতলকাল উরুবেলা সম্প্রদায়ের সঙ্গে কাটান বুদ্ধ। এখানে বেশ কিছু লক্ষণীয় অলৌকিক কাণ্ড ঘটান। জনপ্রিয় স্বর্গীয় প্রতীক এক ভয়ঙ্কর গোখরা সাপকে বশ মানান, ব্রাহ্মণরা যাকে তাঁদের পবিত্র অগ্নিকুণ্ডে স্থাপন করতেন। সমস্ত বনকে অপার্থির ঔজ্জ্বলো ভরিয়ে দিয়ে রাতে তাঁর আস্তানায় বেড়াতে আসা দেবতাদের আনন্দ যোগান তিনি। অগ্নি উৎসের জন্যে অলৌকিক উপায়ে গাছের গুঁড়ি চিরেছেন তিনি, স্বর্গে আরোহণ করে স্বর্গীয় ফুল নিয়ে এসেছেন। উরুবেলা সম্প্রদায়ের নেতা কশ্যপকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি তার অন্তর পড়তে পারেন। পালি টেক্সট ও পরবর্তীকালের জীবনী, উভয়ই প্রথমদৃষ্টিতে যা বিস্ময়কর বুদ্ধের এই ধরনের নিদর্শন ও কেরামতির বিবরণ ধারণ করে। যোগের অনুশীলন দক্ষ যোগিদের বস্তুর ওপর মনের আধিপত্য সৃষ্টির ক্ষমতা (ইদ্ধি) দেওয়ার কথা। কিন্তু তরুণ যোগিদের সাধারণত ইদ্ধির চর্চার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়, কারণ এতে একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তির সামান্য বুজরুকে পরিণত হওয়াটা খুবই সহজ হয়ে পড়ে। স্বয়ং বুদ্ধই এই ধরনের প্রদর্শনবাদীতার তীব্র সমালোচক ছিলেন। প্রকাশ্যে ইদ্ধির চর্চা করার ব্যাপারে অনুসারীদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন তিনি। কিন্তু পালি টেক্সট রচনাকারী সন্ন্যাসীগণ বিশ্বাস করে থাকবেন যে, এই ধরনের কেরামতি সম্ভব ছিল। সম্ভবত ধর্মীয় যুক্তি হিসাবে তাঁরা এইসব কাহিনী ব্যবহার করেছেন। শিক্ষা দানের ক্ষেত্রে টেক্সট রচনাকারী থেরাভেদীয় সন্ন্যাসীগণ হয়তো বুদ্ধের এইসব আকর্ষণীয় ক্ষমতা থাকার কথা বলা সুবিধাজনক মনে করে থাকতে পারেন। এছাড়া, ব্রাহ্মণ ও বৈদিক ধর্মের কর্তাদের সঙ্গে বিতর্কের সময় বুদ্ধ প্রাচীন দেবতাদের বিরুদ্ধে লড়েছেন (আগ্নিকক্ষের পবিত্র গোখরার মতো) বর্ণনা করতে পারাটা উপকারী ছিল; সামান্য ক্ষত্রিয় হলেও ব্রাহ্মণদের ঢের বেশি শক্তি ছিল তাঁর, তিনি তাদের অনায়াসে পরাস্ত করেছেন। পরবর্তীকালে টেক্সট আমাদের বলছে, সমগ্ৰ গোত্ৰ প্রথাকেই চ্যালেঞ্জ করেছেন বুদ্ধ: ‘কেবল জন্মই কাউকে ব্রাহ্মণ বা অস্পৃশ্য করে তোলে না বরং সেটা আমাদের কর্মকাণ্ড (কম্ম)’,[৮] জোর দিয়ে বলেছেন তিনি। ‘নৈতিক আচরণের ওপর ধর্মীয় মর্যাদা নির্ভর করে, জন্মগত দুর্ঘটনার উপর নয়।’ যথারীতি অ্যাক্সিয়েল যুগের অন্য সব মহান সাধুর মতো বুদ্ধ যুক্তি দেখিয়েছেন, বিশ্বাসকে নৈতিকতার সঙ্গে সম্পর্কিত হতে হবে, এটা ছাড়া আচার-আচরণ অর্থহীন।
বুদ্ধের অলৌকিক কর্মকাণ্ড নয়, বরং নৈতিকতাই শেষ পর্যন্ত কশ্যপের বিশ্বাস যুগিয়েছিল। এখানেও টেক্সট হয়তো বোঝাতে চেয়ে থাকতে পারে যে, ইদ্ধির জাঁকাল প্রদর্শনী উল্টো ফল বয়ে আনতে পারে: একজন সংশয়বাদীকে অবশ্যই মুগ্ধ করতে পারেনি। প্রতিটি অলৌকিক ঘটনার পর কশ্যাপ স্রেফ আপন মনে বলেছেন: ‘এই মহান সন্ন্যাসী আকর্ষণীয় ও শক্তিশালী। কিন্তু আমার মতো আরাহান্ত নয়।’ শেষ পর্যন্ত বুদ্ধ তাঁকে অহংকার ও আত্মতুষ্টি হতে বের করে এনেছেন। ‘কশ্যপ,’ বলেছেন তিনি, ‘তুমি আরাহান্ত নও। এভাবে চলতে থাকলে কোনওদিনই আলোকপ্রাপ্ত হতে পারবে না।’ এমন অবাধ অহমবাদ আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে একেবারেই বেমানান। ভর্ৎসনা আঘাত হানল তাঁকে। বিখ্যাত সাধু হিসাবে এজাতীয় আত্মমর্যাদাবোধের বিপদ সম্পর্কে জানা থাকার কথা কশ্যপের। জমিনে আসন পেতে বসে সংঘের সদস্যপদ প্রার্থনা করলেন তিনি। তাঁর অন্য দুভাই ও এক হাজার অনুসারীর প্রত্যেকে তাঁকে অনুসরণ করল। বিপুল সংখ্যক নবীশ দেখা গেল এবার, জটা কামিয়ে পবিত্র তৈজষপত্র ফেলে পরিণত হলো ‘স্রোতে প্রবেশকারী’তে।[৯] এরপর বুদ্ধের তৃতীয় মহান হিতোপদেশ শুনবার জন্যে গয়ায় সমবেত হলো তারা।
‘ভিক্ষুগণ,’ শুরু করলেন বুদ্ধ, ‘সমস্ত কিছু পুড়ছে।’ অনুভূতি ও বাহ্যিক জগৎ, দেহ, মন ও আবেগ, যার ওপর এসব টিকে থাকে, পুড়ছে সমস্ত কিছু। এই অগ্নিকাণ্ডের কারণ কী? লোভ, ঘৃণা ও বিভ্রমের তিনটি অগ্নিকুণ্ড।[১০] মানুষ যতদিন এই শিখাগুলোকে ইন্ধন যোগাবে, ততদিন তা জ্বলতে থাকবে, কখনও নিব্বানার শীতলতা লাভ করবে না। পাঁচটি খণ্ডকে (ব্যক্তিত্বের ‘স্তূপ’ বা ‘উপাদান’) এভাবে আভাসে লাকড়ির ‘বান্ডিলে’র সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। উপাদনা (‘আঁকড়ে’ থাকা) শব্দটার মধ্যেও এক ধরনের পরিহাস রয়েছে, যার মৌল অর্থ ‘জ্বালানি।’[১১] এই জগতের বস্তু সামগ্রী আঁকড়ে থাকার আকাঙ্ক্ষাই আমাদের জ্বালিয়ে রাখে ও আলোকন ব্যাহত করে। যথারীতি এই লোভ ও বাসনা জগতের অশুভ ও সহিংসতার জন্যে দায়ী ঘৃণার সঙ্গে মিশে যায়। অজ্ঞতার তৃতীয় অগ্নিকুণ্ড যতদিন জ্বলবে, মানুষ ততদিন ‘জন্ম, মায়া ও মৃত্যুর দুঃখ, শোক, বেদনা দুঃখ আর হতাশার’[১২] জ্বালাতনকারী চক্র হতে মুক্তির জন্যে আবশ্যক চারটি মহান সত্যি উপলব্ধি করতে পারবে না। সুতরাং ভিক্ষুকে অবশ্যই নিরাসক্ত হয়ে উঠতে হবে। অভিনিবেশের কৌশল তাঁকে তাঁর পাঁচটি খণ্ড হতে বিচ্ছিন্ন হতে শেখাবে; অগ্নিশিখাগুলোকে নিভিয়ে দেবে। তারপর নিব্বানার মুক্তি ও শান্তি প্রত্যক্ষ করবে সে।
অগ্নি-হিতোপদেশ বৈদিক ব্যবস্থার চমৎকার সমালোচনা ছিল। এর পবিত্র প্রতীক অগ্নি বুদ্ধ যেসব জিনিসকে জীবনের পক্ষে ভ্রান্তিপূর্ণ মনে করেছেন তার ইমেজ: অগ্নিকুণ্ড ও বাড়ির প্রতীক যেখান হতে একজন আন্তরিক সন্ধানীকে অবশ্যই ‘অগ্রসর হতে’ হবে। এটা আবার মানুষের চেতনাকে গড়ে তোলা অস্থির, বিধ্বংসী অথচ ক্ষণস্থায়ী শক্তিসমূহেরও চমৎকার প্রতীক। লোভ, ঘৃণা ও অজ্ঞতার তিনটি আগুন বেদের তিন পবিত্র আগুনের বিদ্রূপাত্মক বিপরীত নজীর: এক পুরোহিত গোষ্ঠী গড়ে তোলার ভ্রান্ত বিশ্বাস হতে এগুলোর পরিচর্যা করে ব্রাহ্মণরা স্রেফ তাঁদের আপন অহমবাদেই ইন্ধন যোগাচ্ছিলেন। হিতোপদেশটি ধম্মকে শ্রোতাদের উপযোগি করে তোলায় বুদ্ধের দক্ষতারও প্রকাশ, যেন তিনি তাদের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেন। বুদ্ধের হিতোপদেশ এমন জোরালভাবে তাদের ধর্মীয় চেতনায় সাড়া জাগিয়েছিল যে শোনার পর সাবেক অগ্নি-উপাসকদের সবাই নিব্বানা অর্জন করে আরাহান্তে পরিণত হয়েছিল।
ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ নতুন হাজার ভিক্ষু সঙ্গে নিয়ে মগধের রাজধানী রাজাগহের উদ্দেশে যাত্রা করেন বুদ্ধ। আলোড়ন সৃষ্টি করল তাঁদের আগমন। নতুন আধ্যাত্মিকতার জন্যে ক্ষুধার্ত ছিল নগরবাসীরা। নগর উপকণ্ঠে চারাগাছের বনে নিজেকে বুদ্ধ দাবিকারী এক ব্যক্তি শিণির স্থাপন করেছেন জানতে পেরে রাজা বিম্বিসারা ব্রাহ্মণ গৃহস্থদের বিরাট একটা দল নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। উরুবেলা সম্প্রদায়ের সাবেক প্রধান কশ্যপকে বুদ্ধের অনুসারী রূপে দেখে হতবাক হয়ে গেলেন তাঁরা। কশ্যপের কাছে অগ্নি- উপাসনা ছাড়ার কারণ জেনে দারুণ ক্ষুব্ধ হলেন সবাই। কিন্তু তারা বুদ্ধের বাণী শোনার পর, পালি টেক্সট আমাদের বলছে, ১,২০,০০০ গৃহস্থের সবাই সাধারণ অনুসারীতে পরিণত হলো। সবার শেষে স্বয়ং রাজা বিম্বিসারাও বুদ্ধের সামনে নতজানু হয়ে তাঁকেও সাধারণ অনুসারী করে নেওয়ার আবেদন জানালেন। ছোটবেলা হতেই রাজার আশা ছিল এমন একজন বুদ্ধের প্রচার শুনবেন যাঁর ধম্ম তিনি বুঝতে পারবেন। এবার তাঁর সেই ইচ্ছা পূরণ হলো। এটা ছিল বুদ্ধ ও রাজার দীর্ঘস্থায়ী এক সম্পর্কের সূচনা। সেরাতে বুদ্ধকে তাঁর সঙ্গে খাবার জন্যে আমন্ত্রণ জানান রাজা।
খাবার সময় রাজা সংঘকে এমন এক উপহার দেন যা কিনা বৌদ্ধ সংগঠনের বিকাশের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট প্রভাব রাখবে। ভিক্ষুদের সংঘের আবাস হিসাবে রাজাগহের ঠিক বাইরে বেলুবানার বাঁশ বন নামে পরিচিত একটা প্রমোদ-উদ্যান (আরামা) দান করেছিলেন। সন্ন্যাসীগণ সেখানে নিরিবিলি শান্তি তে বসবাস করতে পারবেন, যেটা আবার যুগপৎ শহর ও মানুষের জন্যে সুগম, যাদের পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন পড়বে। বনটি শহর হতে খুব দূরে বা খুব কাছে ছিল না… মানুষের পক্ষে সুগম, কিন্তু নিরিবিলি, নির্জন।[১৩] উপহার গ্রহণ করলেন বুদ্ধ। চমৎকার সমাধান ছিল এটা। তাঁর সন্ন্যাসীদের ‘বিচ্ছিন্নতা’ মনস্তাত্ত্বিক হওয়ার কথা, জগৎ হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা নয়। সন্ন্যাসীদের ব্যক্তিগত সন্তোষের জন্যে নয়, মানুষের জন্যেই ব্যবস্থার অস্তিত্ব। ধ্যানের জন্যে সন্ন্যাসীদের কিছু মাত্রার শান্ত পরিবেশের প্রয়োজন হবে, যেখানে তাঁরা নিব্বানামুখী নিস্পৃহতা ও অন্তস্থ বিচ্ছিন্নতার বিকাশ ঘটাতে পারবেন, কিন্তু ধম্মের দাবি অনুযায়ী তাঁরা সম্পূর্ণ অন্যদের জন্যে বাঁচতে চাইলে নিজেদের দুঃখ-কষ্ট প্রশমিত করার পদ্ধতি শিখতে সাধারণ মানুষের অবশ্যই তাঁদের কাছে আসার সুযোগ থাকতে হবে। বাঁশ বনের উপহার একটা নজীর স্থাপন করে। ধনী দাতারা প্রায়শঃই সংঘকে শহরতলীর অনুরূপ উদ্যান উপহার দিয়েছে, যা ভবঘুরে ভিক্ষুদের আঞ্চলিক কার্যালয়ে পরিণত হয়েছিল।
নতুন আরামায় দুমাস ছিলেন বুদ্ধ। এই সময়ই তাঁর দুজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুসারী সংঘে যোগ দেন: রাজাগৃহের বাইরে ছোট গ্রামে ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হয়েছিল সারিপুত্ত ও মগ্গালানার। একই দিনে তাঁরা জগত- সংসার ত্যাগ করে সংশয়বাদী সঞ্জয়ের নেতৃত্বাধীন সংঘে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু কেউই পূর্ণ আলোকপ্রাপ্ত হতে পারেননি। তখন তাঁদের ভেতর যে আগে নিব্বানা লাভ করবেন সঙ্গে সঙ্গে অন্যকে জানানোর রফায় পৌঁছেছিলেন তাঁরা। বুদ্ধের আগমনের সময় দুই বন্ধু রাজাগহে বাস করছিলেন। একদিন আশাজিকে (আদি পাঁচ ভিক্ষুর একজন) ভিক্ষা করতে দেখলেন সারিপুত্ত। মুহূর্তে সন্ন্যাসীর প্রশান্তি ও স্থৈর্য্যে ধাক্কা খেলেন তিনি। বুঝে গেলেন, এই মানুষটি আধ্যাত্মিক সমাধান পেয়ে গেছেন। তো প্রচলিত কায়দায় তাঁকে সম্ভাষণ জানিয়ে আশাজির গুরুর পরিচয় ও তিনি কোন ধম্ম অনুসরণ করেন জানতে চাইলেন। পবিত্র জীবনের সামান্য নবীশ হিসাবে নিজেকে তুলে ধরে ধম্মের সারাংশ জানালেন আশাজি। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট ছিল। সেখানেই ‘স্রোতে প্রবেশকারী’তে পরিণত হলেন সারিপুত্ত। মগ্গালানাকে এ সংবাদ পৌঁছে দিতে ছুটলেন দ্রুত। তাঁর বন্ধুও ‘স্রোতে প্রবেশকারী’তে পরিণত হলেন। দুজনে মিলে সংঘে অন্তর্ভুক্ত হবার আবেদন জানাতে সঞ্জয়কে হতাশ করে তাঁর ২৫০ জন শিষ্যকে নিয়ে বাঁশ বনে বুন্ধের কাছে গেলেন তাঁরা। সারিপুত্ত ও মগ্গালানাকে আসতে দেখার সাথে সাথে ওদের প্রতিভা টের পেয়ে গেলেন বুদ্ধ। ‘এরাই হবে আমার প্রধান অনুসারী,’ ভিক্ষুদের বললেন তিনি। ‘সংঘের জন্যে বিরাট ভূমিকা রাখবে ওরা।’[১৪] এবং তাই প্রমাণিত হয়েছিল। বুদ্ধের মৃত্যুর ২০০ থেকে ৩০০ বছরের মধ্যে বিকশিত বৌদ্ধ মতবাদের দুটো প্রধান ধারার প্রেরণাদাতা হয়েছিলেন দুই বন্ধু।[১৫] অধিকতর কঠোর এবং মঠমুখী থেরাভেদা সারিপুত্তকে দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা বিবেচনা করে। বিশ্লেষণী ক্ষমতা ছিল তাঁর। এমনভাবে ধম্মের ব্যাখ্যা দিতে পারতেন যা সহজেই মনে রাখা যেত। কিন্তু তাঁর ধার্মিকতা বৌদ্ধ মতবাদ সম্পর্কে আরও গণতান্ত্রিক দর্শন বিশিষ্ট ও সহানুভূতির ওপর অনেক বেশি গুরুত্ব দানকারী জনপ্রিয় মহায়না ধারার তুলনায় বড় কাঠখোট্টা। মহায়না ধারা মগ্গালানাকে তাদের মন্ত্রণাদাতা হিসাবে গ্রহণ করেছে। ইদ্ধির জন্যে খ্যাত ছিলেন তিনি, অতিন্দ্রীয়ভাবে স্বর্গে আরোহণ করতে পারতেন; যোগ ক্ষমতায় মানুষের মনের কথা বোঝার অলৌকিক ক্ষমতা ছিল তাঁর। বুদ্ধের সারিপুত্ত ও মগ্গালানার উভয়ের প্রশংসা থেকে বোঝা যায় দুটো মতবাদকেই সঠিক মনে করা হয়েছে। এবং প্রকৃতপক্ষেই ক্রিশ্চান জগতের ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যান্টদের চেয়ে ঢের শান্তিপূর্ণভাবে সহাবস্থান করেছে ওরা।
সবাই অবশ্য বুদ্ধের প্রেমে পড়েনি। বাঁশ বাগানে অবস্থান কালে রাজাগহের বহু অধিবাসী বোধগম্য কারণেই সংঘের নাটকীয় সমৃদ্ধিতে উদ্বিগ্ন বোধ করেছে। প্রথমে জটাধারী ব্রাহ্মণ, এবার সঞ্জয়ের সংশয়ীরা–এরপর কে? সমস্ত তরুণ-যুবাকে কেড়ে নিয়ে গৌতম সন্ন্যাসী সবাইকে সন্তানহীন ও নারীদের বিধবায় পরিণত করছেন। অচিরেই তাদের সংসার বিনষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু প্রসঙ্গটি বুদ্ধের গোচরে আনা হলে তিনি ভিক্ষুদের চিন্তা করতে নিষেধ করলেন: এটা স্রেফ সাতদিনের একটা বিস্ময় এবং নিশ্চিতভাবে সপ্তাহ খানেকের মধ্যে সমস্যা মিটে গিয়েছিল।[১৬]
পালি টেক্সট আমাদের বলছে, এই সময় কাপিলাবাস্তুতে বাবার বাড়িতে গিয়েছিলেন বুদ্ধ–তবে আমাদের বিস্তারিত কিছু জানায় না। অবশ্য, পরবর্তী সময়ের ধর্মগ্রস্থ ও ধারাভাষ্যগুলো পালি টেক্সটের কংকালে রক্ত-মাংস জুড়েছে; এইসব উত্তর-শাস্ত্রীয় কাহিনী বুদ্ধের কিংবদন্তীর অংশে পরিণত হয়েছে।[১৭] এসব আমাদের বলে, শুদ্ধোদন তাঁর ছেলে, এখন বিখ্যাত বুদ্ধ রাজাগহে ধর্ম প্রচার করছেন জানতে পেরে বিরাট এক প্রতিনিধিদলসহ বার্তাবাহক পাঠিয়ে কাপিলা-বাস্তুতে অতিথি হবার আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু বুদ্ধের বক্তব্য শোনার পর শাক্যদের এই মিছিলের সবাই শুদ্ধোদনের বার্তার কথা ভুলে গিয়ে আরাহান্তে পরিণত হয়– এমন ঘটনা সাতবার ঘটেছিল। অবশেষে বুদ্ধকে আমন্ত্রণ পৌঁছে দেওয়া হলো। বিশ হাজার ভিক্ষু নিয়ে নিজ শহরের উদ্দেশে রওনা হলেন তিনি। শাক্যরা কাপিলাবাস্তুর বাইরে নিগরোধা বাগান ভিক্ষুদের হাতে ছেড়ে দেয়। শাক্যের সংঘের প্রধান কার্যালয়ে পরিণত হয় তা। কিন্তু শাক্যরা অহংকার ও ঔদ্ধত্য দেখিয়ে বুদ্ধকে সম্মান জানাতে অস্বীকার করে। ফলে, কথিত আছে, তাদের পর্যায়ে অবতরণ করে ইদ্ধির আকর্ষণীয় চমক তুলে ধরেন বুদ্ধ। শূন্যে ভাসলেন তিনি, হাত-পা হতে আগুন ও পানির ধারা বের হলো এবং সবশেষে আকাশের বুকে রত্নখচিত পথে হাঁটলেন। সম্ভবত অভ্যাসবশত শাক্যদের বোধগম্য ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করছিলেন তিনি, তাদের মনের ভেতর প্রবেশ করতে চেয়েছেন। বাবা শুদ্ধোদন চেয়েছিলেন তিনি যেন বিশ্বশাসক চক্কবত্তী হন; এই কিংবদন্তীর চরিত্রও, কথিত আছে, রাজকীয় ঢঙে আকাশে ঘুরে বেড়াতে পারেন। উরুবেলায় বুদ্ধ ব্রাহ্মণ সাধকদের কাছে নিজেকে যেকোনও চক্কবত্তীর চেয়ে শ্রেয় করে তুলে ধরেছিলেন। প্রদর্শনীয় প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিল তাতে, যদিও তা ছিল বাহ্যিক। শাক্যরা হতবাক হয়ে গিয়েছে। বুদ্ধের সামনে মাথা নত করেছে।
কিন্তু যথারীতি ইদ্ধি স্থায়ী ফল বয়ে আনতে পারেনি। পরদিন কাপিলাবাস্তুতে ছেলেকে খাবার মাংতে দেখে দারুণ পিড়ীত বোধ করলেন শুদ্ধোদন: পরিবারের মর্যাদার এমন অসম্মান করার সাহস তিনি পেলেন কোথায়? কিন্তু বাবার কাছে ধৰ্ম্ম ব্যাখ্যা করলেন বুদ্ধ। কোমল হলো শুদ্ধোদনের হৃদয়। নিমেষে ‘স্রোতে প্রবেশকারী’ তে পরিণত হলেন তিনি, যদিও সংঘে যোগদানের আবেদন জানাননি। বুদ্ধের কাছ থেকে পাত্র নিয়ে ঘরে নিয়ে এলেন তাঁকে। এখানে তাঁর সম্মানে প্রস্তুত খাবার গ্রহণের সময় একটা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম বাদে বাড়ির সব মহিলা তাঁর সাধারণ শিষ্যে পরিণত হয়। বুদ্ধের সাবেক স্ত্রী দূরে সরে রইলেন, সম্ভবত বোধগম্যভাবেই কোনওরকম কথাবার্তা ছাড়াই তাঁকে ত্যাগ করে যাওয়া মানুষটির প্রতি তখনও বৈরী ভাবাপন্ন ছিলেন তিনি।
পালি টেক্সটসমূহ ধারণ করেছে যে, কাপিলাবাস্তু সফরের পর অনির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর শাক্যের নেতৃস্থানীয় যুবকেরা গৃহ ত্যাগ করে সংঘে যোগ দেন। বুদ্ধের সাত বছর বয়সী ছেলে রাহুলাও ছিলেন সেই দলে। দীক্ষা নেওয়ার আগে বিশ বছর বয় পূর্ণ হওয়া অপেক্ষা করতে হয়েছিল তাঁকে। বুদ্ধের তিন নিকটাত্মীয়ও ছিলেন: তাঁর চাচাত ভাই আনন্দ; সৎভাই নন্দ ও শ্যালক দেবদত্ত। নাপিত উপলও সঙ্গী হয়েছিল তাঁদের। নতুন ভিক্ষুদের মাথা মোড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাকে, কিন্তু সেও যোগদানের আবেদন জানায়। সঙ্গীরা আগে নাপিতকে দীক্ষা দিতে বলেছেন যাতে তাদের শাক্য অহংকার চূর্ণ হয়।[১৮] এই শাক্যদের কেউ কেউ সংগঠনের উল্লেখযোগ্য চরিত্রে পরিণত হয়েছেন। উপল হয়ে ওঠে মঠ-জীবনের নিয়ম-কানুনের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় বিশেষজ্ঞ। সজ্জন, বিবেকবান আনন্দ পরিণত হন বুদ্ধের জীবনের শেষ বিশ বছরের ব্যক্তিগত পরিচারক। আনন্দ অন্য যেকারও থেকে বুদ্ধের অনেক ঘনিষ্ঠ ছিলেন; প্রায় সর্বক্ষণিক সাহচর্যে থাকার সুবাদে বুদ্ধের হিতোপদেশ ও বাণীর ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু দক্ষ যোগি ছিলেন না তিনি। ধম্মের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অভিজ্ঞ কর্তৃপক্ষে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও ধ্যানের ক্ষমতা না থাকায় বুদ্ধের জীবদ্দশায় নিব্বানা লাভ করেননি। দেবদত্তের ক্ষেত্রে আমরা যেমন দেখি, ধর্মগ্রস্থসমূহ তাকে গস্পেল কাহিনীর জুডাসের অনুরূপ ভূমিকা দিয়েছে।
জেসাসের অনুসারীদের বর্ণাঢ্য উপস্থাপনসহ গস্পেলের উল্লেখ পশ্চিমা পাঠকদের মনে আদি এইসব বৌদ্ধদের সম্পর্কে আরও জানতে আগ্রহী করে তোলে। হাজারে হাজারে সংঘে যোগ দেওয়া এই মানুষগুলো কারা ছিল? বুদ্ধের কাছে কীসের আকর্ষণে ছুটে এসেছিল তারা পালি টেক্সট সে সম্পর্কে সামান্যই জানায় আমাদের। কিংবদন্তী আভাস দেয় যে, ‘বহুজনের’ কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়া হলেও ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় গোত্র হতে এসেছিল প্রথম যোগদানকারীরা। সবাই যোগদানের আহ্বান পেয়েছিল: বণিকরাও সংগঠনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। সন্ন্যাসীদের মতো তারাও বিকাশমান সমাজের ‘নতুন মানুষ’ ছিল। আবশ্যিকভাবে গোত্র বর্জিত সমাজের প্রতিনিধিত্বকারী একটা বিশ্বাসের প্রয়োজন ছিল তাদের। তবে গস্পেল যেমন জেলেদের জাল ছাড়া ও কর সংগ্রাহকদের বাড়ি ছাড়ার কথা বলে সে রকম ব্যক্তিগত ধর্মান্তরের কোনও বিস্তারিত কাহিনী নেই। ভিক্ষুদের মাঝে অনন্য হয়ে আছেন আনন্দ ও দেবদত্ত, কিন্তু জেসাসের কিছু অনুসারীর আরও ব্যাপক বিবরণের তুলনায় তাদের কাহিনীও প্রতীকী ও বিশেষ রীতি অনুসারী। এমনকি বুদ্ধের নেতৃস্থানীয় শিষ্য সারিপুত্ত ও মাগ্গালানাকেও দৃশ্যতঃ সামান্য ব্যক্তিত্বপূর্ণ মলিন চরিত্র হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। ছেলের সঙ্গে বুদ্ধের সম্পর্ক নিয়েও কোনও মর্মস্পশী আখ্যান নেই: পালি টেক্সটে রাহুলা স্রেফ আরেক জন সন্ন্যাসী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছেন। তাঁকে ধ্যানের শিক্ষা দিয়েছেন বুদ্ধ, অন্য যেকোনও ভিক্ষুর ক্ষেত্রে যেমনটি করতেন তিনি। বিবরণে তাঁরা যে পিতা-পুত্র এমনটি বোঝানোর মতো কিছু নেই। ইমেজ পাই আমরা, কোনও ব্যক্তিত্ব নয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রতি পাশ্চাত্য অনুরাগের কারণে আমরা অসন্তুষ্ট বোধ করি।
কিন্তু তাতে বৌদ্ধদের অভিজ্ঞতার প্রকৃতিকে ভুল বোঝা হবে। আদি এই সন্ন্যাসীদের অনেকেই কেবল অনাত্মার মতবাদ অনুধ্যান করে আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এটা তাদের সত্তার উর্দ্ধে যেতে সক্ষম করেছে। আসলে স্থায়ী ব্যক্তিত্ব বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব থাকার কথা অস্বীকার করেছেন বুদ্ধ। তিনি সত্তাবোধের কোনও পবিত্র, নূন্যতম বস্তুর প্রতি অটল বিশ্বাসকে আমাদের আলোকনের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো ‘অদক্ষ’ বিভ্রান্তি মনে করতেন। অনাত্মার আধ্যাত্মিকতার ফলে খোদ বুদ্ধ পালি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যক্তি না হয়ে বরং একটা ধরণ হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছেন। অন্যান্য ধরনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তিনিঃ সংশয়বাদী, ব্রাহ্মণ ও জৈন। পশ্চিমা মানুষ যেসব অসাধারণ গুণ ও বৈশিষ্ট্যকে আদর্শ হিসাবে কদর করে ঠিক সেগুলোর বিলুপ্তি ঘটিয়েই মুক্তি অর্জন করেছেন তিনি। শিষ্যদের বেলায়ও একই কথা খাটে। ভিক্ষুদের সাথে বুদ্ধের পার্থক্য টানার মতো কিছু নেই, তাঁদের ক্ষুদ্র বুদ্ধ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বুদ্ধের মতো তাঁরাও নৈর্ব্যক্তিক হয়ে গেছেন, ব্যক্তি হিসাবে বিলীন হয়ে গেছেন। অনুমোদিত টেক্সট তাঁদের মনের গভীরে যেতে অস্বীকার জানিয়ে এই পরিচয়হীনতা সংরক্ষণ করেছে; এসব আলোকন প্রাপ্তির আগে তাঁদের চরিত্রের কোনও পছন্দযোগ্য আচরণও প্রকাশ করবে না। দেবদত্ত ও আনন্দের সাধারণের চেয়ে ভিন্ন হওয়াটা দুর্ঘটনা নাও হতে পারে। দেবদত্ত অহমবাদে পরিপূর্ণ, এবং আনন্দ আলোকপ্রাপ্ত হতে ব্যর্থ হওয়ায় পরিণামে সরিপুত্তের মতো আধ্যাত্মিক মহাপুরুষের চেয়ে বেশি লক্ষযোগ্য ব্যক্তিগত গুণের অধিকারী ছিলেন। বুদ্ধের জীবনের শেষ ভাগে আমরা আনন্দের মহৎ হৃদয় সম্পর্কে আরও জানতে পারি, কিন্তু আমরা যেমন দেখব, তিনি বুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গির অংশীদার হতে পারেননি। ব্যক্তিত্বের এমনি বিনাশে বিলাপকারী কোনও পশ্চিমাবাসীকে ভিক্ষুরা সম্ভবত জানাতেন যে নিব্বানার অন্তস্থ শাস্তি লাভের জন্যে অহম বিসর্জনই যথার্থ মূল্য, সত্তাবোধে বন্দি কারও পক্ষে যা সম্ভবত অসম্ভব।
কিন্তু বুদ্ধ এবং তাঁর শিষ্যদের নৈর্ব্যক্তিক ভাবে এর মানে এই নয় যে তাঁরা শীতল, অনুভূতিহীন ছিলেন। তাঁরা কেবল সহানুভূতি সম্পন্ন ও সজ্জনই ছিলেন না, গভীরভাবে সামাজিকও ছিলেন। তাঁদের ‘বহুজনের’ কাছে পৌঁছানোর প্রয়াস মানুষকে আকৃষ্ট করেছে, অহমবাদের অভাব অপ্রতিরোধ্য মনে হয়েছে তাদের।
সকল সন্ন্যাসীর মতো অবিরাম চলার উপর থাকতেন বুদ্ধ। যতদূর সম্ভব বৃহৎ দর্শকের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতেন, কিন্তু বর্ষা মৌসুমের তিন মাসে চলাচল কঠিন হয়ে গেলে রাজাগহের বাইরে বাঁশ বাগানেই অবস্থান করতেন। উদ্যানটি এখন সংঘের মালিকানাধীন হলেও ভিক্ষুরা সেখানে কোনও কিছু নির্মাণ না করে খোলা মাঠেই অবস্থান করতেন। যাহোক এক ধনী বর্ণিক বাঁশ বন বেড়াতে এসে জায়গাটা পছন্দ করে ফেললেন, সন্ন্যাসীদের জন্যে ষাটটি কুটির নির্মাণ করে দেওয়ার প্রস্তাব দিলেন তিনি। অনুমতি দিলেন বুদ্ধ। এরপর বুদ্ধ এবং সন্ন্যাসীদের খাবারে আমন্ত্রণ জানালেন বণিক। এমন বিশাল জমায়েতকে খাওয়ানো সামান্য ব্যাপার ছিল না। খাবারের দিন সকালে কাজের লোকেরা জাউ, ভাত, ঝোল ও মিষ্টি বানানোর সময় গোটা বাড়ি শোরগোলে ভরে উঠেছিল। বণিক মহাশয় নানা কাজ ও ফরমাশ দিতে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে ব্যবসায়িক কাজে সাবস্তি থেকে রাজাগহে আগত শ্যালক অনাথাপিন্দিকাকে স্বাগত জানানোরও ফুরসত পাননি। ‘হচ্ছেটা কী?’ সবিস্ময়ে জানতে চাইলেন অনাথাপিন্দিকা। সাধারণত এ বাড়িতে বেড়াতে এলে ভগ্নিপতি তার সমাদর করে কুলিয়ে উঠতে পারেন না। বিয়ে জাতীয় কিছু হচ্ছে? নাকি রাজা বিম্বিসারাকে আপ্যায়ন করা হচ্ছে? ‘মোটেই তা নয়,’ জবাব দিলেন বণিক I বুদ্ধ ও তাঁর সন্ন্যাসীরা খেতে আসছেন।
নিজের কানকে বিশ্বাস করে উঠতে পারলেন না অনাথাপিন্দিকা। ‘কী বললে, বুদ্ধ?’ অবিশ্বাসের সুরে জানতে চাইলেন তিনি। সত্যি কি একজন আলোকপ্রাপ্ত বুদ্ধ আবির্ভূত হয়েছেন এই জগতে? তিনি কী এখনই তাঁর সাথে দেখা করতে যেতে পারেন? ‘এখন তার উপযুক্ত সময় নয়,’ তীর্যক কণ্ঠে জবাব দিয়ে ফের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বণিক। ‘কাল ভোরে তাঁর সাথে কথা বলতে পারবে।’ অনাথাপিন্দিকা এমনই উত্তেজিত ছিলেন, বলতে গেলে রাতে ঘুমাতে পরলেন না তিনি। খুব ভোরে বাঁশ বাগানের পথ ধরলেন তিনি। কিন্তু নগর থেকে বের হয়ে আসার পরপরই অ্যাক্সিয়াল যুগের সাধারণ ভীতিতে প্রবলভাবে আক্রান্ত হলেন। নিজেকে নাজুক মনে হলো তাঁর। ‘জগৎ থেকে আলো হারিয়ে গেল, সামনে কেবল অন্ধকার দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি।’ ভোরের আলোয় বুদ্ধকে পায়চারিরত অবস্থায় না দেখা অবধি ভয়ে ভয়ে আগে বাড়লেন তিনি। অনাথাপিন্দিকাকে দেখে তাঁকে বসতে দিলেন বুদ্ধ, নাম ধরে ডাকলেন। অতীতের ইয়াসার মতোই নিমেষে প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন বণিক; বুদ্ধে কথা শোনার সাথে সাথে এমন প্রবলভাবে তাঁর শিক্ষা জেগে উঠতে শুরু করল যেন তাঁর আত্মার গভীরে তা খোদাই হয়েছিল। ‘অসাধারণ, প্রভু!’ চিৎকার করে বলে উঠলেন তিনি। বুদ্ধের কাছে তাঁকে একজন শিষ্য করে নেওয়ার আবেদন জানালেন। পরদিন ভগ্নিপতির বাড়িতে বুদ্ধকে আপায়ন করলেন তিনি। নিজ শহর কোসালার রাজধানী সাবস্তি সফরের আমন্ত্রণ জানালেন তাঁকে।[১৯]
ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পাদে সাবস্তি সম্ভবত গাঙ্গেয় উপত্যকার সবচেয়ে অগ্রসর শহর ছিল। রিবতি নদীর দক্ষিণ পাড়ে দুটো বাণিজ্য পথের মিলনস্থলে গড়ে উঠেছিল শহরটি। প্রায় ৭০,০০০ পরিবারের আবাস ছিল এখানে। নেতৃস্থানীয় বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে অনাথাপিন্দিকার মতো বহু ধনী ব্যবসায়ী এখানে বাস করত। কথিত আছে, শহরের নাম ‘সর্বমাস্তি’ হতে নেওয়া, কেননা এটা এমন এক জায়গা ছিল যেখানে ‘সবকিছুই পাওয়া সম্ভব’। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ফুট উঁচু দর্শনীয় টাওয়ারে সুরক্ষিত সাবস্তির প্রধান সড়কগুলো দক্ষিণ দিক থেকে শহরে এসে শহর কেন্দ্রের একটা খোলা চত্বরে মিলিত হয়েছে।[২০] কিন্তু সাবস্তির সমৃদ্ধি সত্ত্বেও একজন সত্যিকার বুদ্ধের সঙ্গে সাক্ষাতের সম্ভাবনায় অনাথাপিন্দিকার উত্তেজনা বহু মানুষের জীবনের এক অস্বস্তিকর শূন্যতার অনুভূতি তুলে ধরে। সংঘের জন্যে জুৎসই জায়গা।
বুদ্ধের জন্যে একটা ঘাঁটি নির্মাণে কোনও রকম ব্যয়ে কণ্ঠিত হলেন না অনাথাপিন্দিকা। জুৎসই একটা জায়গার খোঁজে কঠোর পরিশ্রম করেছেন তিনি। অবশেষে কোসালার সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী রাজকুমার জিতের একটা উদ্যান বেছে নিলেন। অনাথাপিন্দিকা ঠেলাগাড়ি ভর্তি করে সোনার মোহর আনার আগে পর্যন্ত বিক্রিতে অনীহ ছিলেন রাজপুত্র। মোহরগুলো সারা বাগানে ছড়িয়ে দিলেন তিনি, গোটা জমিন ঢাকা পড়ে গেল তাতে। এত টাকা দিতে রাজি ছিলেন তিনি। কেবল প্রবেশ পথের কাছে সামান্য একটু জায়গা বাকি ছিল। দেরিতে হলেও রাজকুমার জিত বুঝতে পারলেন, কোনও মামুলি লেনদেন নয় এটা। চাঁদা দেওয়াটা সুবিধাজনক হতে পারে। ফলে সেই জায়গাটুকু বিনামূল্যে ছেড়ে দিলেন। সেখানে একটা গেইট-হাউস নির্মাণ করে দিলেন। তারপর জিতের উদ্যানকে সংঘের জন্যে তৈরি করে দিলেন অনাথাপিন্দিকা। তিনি ‘উন্মুক্ত কুটির নির্মাণ করালেন, তোরণ বানালেন, নির্মাণ করালেন দর্শক মহল, অগ্নিকক্ষ, গুদাম ও স্নানাগার তৈরি করালেন, পুকুর কাটালেন, তাঁবু খাটালেন।’[২১] সংঘের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হবে এটা।
কিন্তু ‘গৃহহীনতা’কে আলিঙ্গনকারী মানুষের পক্ষে খুবই জাঁকাল আয়োজন ছিল এসব। খুবই কম সময় পরিসরে রাজাগহ কাপিলাবাস্তু ও সাবস্তিতে পদ্মপুকুর, অসংখ্য আম গাছ আর ছায়াময় নারকেল সারিতে ঘেরা তিনটি বিরাট উদ্যানের মালিক হয়েছেন বুদ্ধ যেখানে সন্ন্যাসীরা বসবাস ও ধ্যান করতে পারবেন। অন্য দাতাগণ দ্রুত অনাথাপিন্দিকার নজীর অনুসরণ করলেন। বুদ্ধ সাবস্তিতে ধম্ম প্রচার করছেন জেনে যমুনা তীরের কোসাম্বির তিন মহাজন তাঁর বয়ান শুনতে জিতের উদ্যানে হাজির হলেন এবং তাঁকে স্ব স্ব শহরে আমন্ত্রণ জানালেন। প্রত্যেকে যার যার শহরে একটি করে ‘প্রমোদ উদ্যান’ (আরামা) নির্মাণ করলেন। কেবল নিজেদের পয়সা খরচ করে দালান কোঠাই নির্মাণ করলেন না তাঁরা, বরং অন্যান্য দাতার মতো নিজেরাই খরচ যুগিয়ে আরামার সংরক্ষণও করেছেন তাঁরা। বাঁশ বাগান পরিচর্যায় রাজা বিম্বিসারা এত লোক নিয়োজিত করেছিলেন যে গোটা গ্রাম পূর্ণ করে ফেলেছিল তারা। কিন্তু সন্ন্যাসীরা বিলাসিতায় বাস করেননি। প্রচুর হলেও আয়োজন ছিল সাধারণ। কুঁড়েগুলোয় মধ্যপন্থীদের উপযোগি আসবাবের অতিরিক্ত তেমন কিছু ছিল না। প্রত্যেক ভিক্ষুর ভিন্ন সেল ছিল, কিন্তু প্রায়শঃই সেটা ছিল পার্টিশন দিয়ে আলাদা করা একটা জায়গা, ঘুমানোর জন্যে স্রেফ একটা পাটাতন আর বসার জন্যে জোড়া দেওয়া পায়াঅলা একটা আসন থাকত সেখানে।[২২]
ভিক্ষুগণ সারা বছর এইসব আরামায় থাকতেন না, বরং বেশিরভাগ সময় পথেই কাটাতেন তাঁরা। গোড়ার দিকে অধিকাংশই বর্ষাকালেও চলার উপর থাকতেন, কিন্তু পরে এটা আঘাতকারী হিসাবে আবিষ্কার করেন। জৈনদের মতো অন্য গোত্রগুলো বৃষ্টির সময় পথ চলতে অস্বীকার করেছে, কারণ তাতে বুনোজীবনের ক্ষতি হবে এবং অহিংসার নীতি লঙ্ঘিত হবে। লোকে প্রশ্ন করতে শুরু করেছিল, শাক্যমুনির শিষ্যরা কেন বর্ষাকালে ভ্রমণ অব্যাহত রেখেছে? ‘কাচি ঘাস মাড়াচ্ছে, গাছপালা নষ্ট করছে, অসংখ্য ক্ষুদে প্রাণীকে কষ্ট দিচ্ছে?’ এমনকি শকুনের ঝাঁকও তো, যুক্তি দেখিয়েছে তারা, বর্ষার সময় গাছে বসে থাকে। কেন কেবল বুদ্ধের সন্ন্যাসীরা কারও কথা কানে না তুলে নিজেদের কর্দমাক্ত পথঘাটে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য মনে করেন?[২৩]
এই জাতীয় সমালোচনায় স্পর্শকাতর ছিলেন বুদ্ধ। এইসব অভিযোগ শুনতে পেয়ে মৌসুমি বিশ্রামকে (বাস্যা) সংঘ সদস্যদের জন্যে বাধ্যতামূলক করে দিলেন তিনি। কিন্তু অন্য ভবঘুরেদের চেয়ে আরেক কদম অগ্রসর হয়ে তিনি মঠচারী গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন শুরু করলেন। অন্যান্য গোত্রের সন্ন্যাসীগণ বাস্যার সময়ে একাকী বাস করতেন বা যেখানে থাকতেন সেখানেই সম্পূর্ণ ভিন্ন ধৰ্ম্ম অনুসারী সন্তদের সঙ্গে বনের কোনও ফাঁকা জায়গায় সময় কাটাতেন। অন্যান্য গোত্রের সদস্যদের সঙ্গে নয়, বাস্যার সময় সন্ন্যাসীদের একসঙ্গে থাকবার নির্দেশ দিলেন বুদ্ধ। তারা যেকোনও আরামা বা প্রতি বছর শূন্য হতে গড়ে তোলা কোনও পল্লী বসতি (আবাসা) বেছে নিতে পারতেন। প্রতিটি আরামা ও আবাসার নির্ধারিত সীমানা ছিল। জোরাল কোনও কারণ ছাড়া বর্ষার তিনমাস কোনও সন্ন্যাসীর সপ্তাহকালের বেশি সময়ের জন্যে বিশ্রাম ত্যাগ করার অনুমতি ছিল না। ক্রমে সন্ন্যাসীগণ একটা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন গড়ে তুলতে লাগলেন। সহজ সাধারণ অনুষ্ঠান সৃষ্টি করলেন তাঁরা। তাঁদের বসতির মিলন কক্ষে এসবের আয়োজন করা হতো। সকালে ধ্যান করতেন তাঁরা, কিংবা অন্য কোনও প্রধান সন্ন্যাসীর নির্দেশনা শুনতেন। তারপর দিনের রসদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যার যার পাত্র নিয়ে শহরের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়তেন। দিনের মূল খাবার গ্রহণ করতেন। বিকেলে চলত বিশ্রাম, সন্ধ্যায় আয়োজন করা হতো আরও ধ্যানের।
কিন্তু সবার ওপরে ভিক্ষুগণ আন্তরিকতার সঙ্গে বাস করতে শিখেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে হয়তো পছন্দ হবে না এমন মানুষের সঙ্গে সহবাস করার অনিবার্য সমস্যাগুলো ধ্যানের মাধ্যমে যে প্রশান্তি অর্জন করার কথা তাকে পরীক্ষার সম্মুখীন করত। ভিক্ষুরা পরস্পরের প্রতি সমব্যাথী না হতে পারলে পৃথিবীর চারদিকে সহানুভূতি প্রেরণ শুভকর হতো না। বুদ্ধ সন্ন্যাসীদের শাস্তি দিয়েছেন, এমন ঘটনাও আছে। একবার পেটের পীড়ায় আক্রান্ত ভিক্ষুর যত্ন নিতে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁদের ভর্ৎসনা করছেন তিনি।[২৪] আরেকবার বুদ্ধ ও তাঁর সফরসঙ্গীরা সাবস্তি ভ্রমণ করার সময় সন্ন্যাসীদের ক্ষুদে একটা দল আগেভাগে স্থানীয় এক বসতিতে গিয়ে সবগুলো বিছানা দখল করে নিয়েছিলেন। প্রবল কাশিতে ভুগছিলেন সারিপুত্ত, সারারাত গাছের নিচে কাটাতে হয়েছিল তাঁকে। এমন নিষ্ঠুরতা, অপরাধী সন্ন্যাসীদের বলেছেন বুদ্ধ, সংঘের সামগ্রিক উদ্দেশ্যকে খাট করেছে। কেননা এতে মানুষ ধম্ম হতে দূরে সরে যাবে।[২৫] কিন্তু আস্তে আস্তে সেরা ভিক্ষুরা তাঁদের নিজস্ব স্বার্থপর প্রবণতা বিসর্জন দিয়ে সতীর্থদের কথা বিবেচনা করতে শিখেছেন। ভিক্ষা নিয়ে শহর থেকে প্রথম প্রত্যাবর্তনকারী অন্যদের জন্যে কুটির গোছাতেন, আসন সাজাতেন ও রান্নার পানি যোগাড় করে রাখতেন। সবার শেষে যিনি বাড়ি ফিরতেন তিনি উচ্ছিষ্ট খেয়ে এঁটো থালাবাসন গুছিয়ে রাখতেন। ‘দেহের দিক দিয়ে আমরা একেবারে আলাদা, প্রভু,’ সম্প্রদায় সম্পর্কে বুদ্ধকে বলেছিলেন একজন সন্ন্যাসী। ‘কিন্তু মনে হয় আমাদের মন একটাই।’ কেন আপন পছন্দ-অপছন্দ উপেক্ষা করে অন্যদের ইচ্ছানুযায়ী চলবেন না তিনি? এমন সঙ্গীদের সঙ্গে পবিত্র জীবন কাটাতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করেছেন এই ভিক্ষু।[২৬] বাস্যার গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে সন্ন্যাসীদের অপরের জন্যে বাঁচতে শেখানোর নতুন উপায় আবিষ্কার করেছিলেন বুদ্ধ।
বৌদ্ধদের আরামার বন্ধুসুলভ ও আনন্দময় জীবন দেখে খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন কোসালার রাজা পাসেনেদি। রাজ দরবারের সম্পূর্ণ উল্টো, বুদ্ধকে বলেছিলেন তিনি, যেখানে স্বার্থপরতা, লোভ ও আগ্রাসনই দস্তুর। এক রাজা অন্য রাজার সঙ্গে ঝগড়া করেন, ব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণদের সঙ্গে। পরিবার ও বন্ধুবান্ধব সারাক্ষণ ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত। কিন্তু আরামায় তিনি ভিক্ষুদের দুধ আর পানির মতো বিবাদহীন জীবন কাটাতে দেখেছেন, দয়ার্দ্র দৃষ্টিতে পরস্পরকে দেখেছেন তাঁরা।’ অন্যান্য ক্ষেত্রে সাধকদের শীর্ণ ও দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থায় দেখে মনে হয়েছে, জীবনধারা তাদের সঙ্গে খাপ খায়নি। ‘কিন্তু আমি দেখছি ভিক্ষুরা হাসছেন, ভদ্র, আন্তরিকভাবেই সুখী…স্বজনরা, শান্ত, অবিচলিত, ভিক্ষা করে জীবিকা নির্বাহ করছেন, তাদের মন বুনো হরিণের মতোই কোমল রয়ে গেছে।’ মন্ত্রণা সভায় বসলে, কৃশ কণ্ঠে বলেছেন রাজা, বারবার বাধা দেওয়া হয় তাঁকে, এমনকি উত্যক্ত করা হয়; কিন্তু বুদ্ধ সন্ন্যাসীদের বিশাল জমায়েতের উদ্দেশে বক্তব্য রাখার সময় কেউ এমনকি কাশি বা গলা খাকারিও দেয় না।[২৭] জীবনের এক বিকল্প ধারা নির্মাণ করছিলেন বুদ্ধ যা নতুন শহর ও রাজ্যের ঘাটতিসমূহকে স্পষ্ট করে তুলেছিল।
কোনও কোনও পণ্ডিত বিশ্বাস করেন, পাসেনেদি ও বিম্বিসারার মতো শাসকদের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার কর্মসূচির সহযোগি হিসাবে দেখেছেন বুদ্ধ। তাঁরা মত প্রকাশ করেছেন, সমাজ এক গোত্রীয়, গোষ্ঠী ভিত্তিক রীতিনীতি হতে প্রতিযোগিতামূলক, গলাকাটা রাজার অর্থনীতির দিকে অগ্রসর হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে অনিবার্য ক্রমবর্ধমান ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদকে মোকাবিলা করার জন্যেই সংঘের নকশা করা হয়েছিল। এক ভিন্ন ধরনের সামাজিক সংগঠনের নীলনকশায় পরিণত হবে সংঘ এবং এর ধারণাসমূহ ক্রমে জনগণের কাছে পৌঁছে যাবে। টেক্সটে বুদ্ধ ও চক্কবত্তীর ঘনঘন পাশাপাশি উপস্থাপনের দিকে ইঙ্গিত করেছেন তাঁরা: বুদ্ধ মানবীয় চেতনাকে সংস্কার করবেন, অন্য দিকে রাজাগণ সামাজিক সংস্কারের সূচনা ঘটাবেন।[২৮] অতি সাম্প্রতিকালে অন্যান্য পণ্ডিত অবশ্য যুক্তি দিয়েছেন যে, রাজতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতা দূরে থাক, তিনি বরং এভাবে কাজ করার বেলায় যারপরনাই সমালোচনামুখর ছিলেন; নিজ রাজ্য শাক্যে চলমান প্রজাতন্ত্র ধরনের সরকারই পছন্দ করতেন।[২৯]
বুদ্ধের এমন রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল বলে মনে হয় নাঃ যে কোনও সামাজিক কর্মসূচির সঙ্গে জড়িত থাকাকে নির্ঘাৎ জাগতিক বিশ্বকে ‘আঁকড়ে’ থাকার মতো অনুপযোগি মনে করতেন তিনি। তবে বুদ্ধ অবশ্যই মানুষ হবার একটা নতুন উপায় উদ্ভাবনের প্রয়াস পাচ্ছিলেন। ভিক্ষুদের স্পষ্ট সন্তুষ্টি দেখায়, তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষা ফলপ্রসু হয়েছিল। সন্ন্যাসীগণ অতিপ্রাকৃত করুণায় পরিপূর্ণ হননি বা কোনও দেবতার অনুগ্রহে সংস্কৃত হননি, বুদ্ধের আবিষ্কৃত পদ্ধতি সম্পূর্ণ মানবীয় উদ্যোগ ছিল। তাঁর সন্ন্যাসীগণ দক্ষতার সঙ্গে স্বাভাবিক ক্ষমতা কাজে লাগাতে শিখছিলেন যেমন করে কোনও কামার এক টুকরো ধাতুকে চকচকে ও সুন্দর করে তুলবে এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ ও পূর্ণ সম্ভাবনায় বিকশিত হতে সাহায্য করবে। মনে হয় মানুষকে নিঃস্বার্থভাবে বাঁচতে ও সুখী হওয়ার শিক্ষা দেওয়া সম্ভব ছিল। ভিক্ষুরা বিষণ্ন বা হতাশ হয়ে থাকলে বোঝাত যে, তাঁদের জীবনধারা মানবীয় সত্তার প্রতি নিপীড়ন চালাচ্ছে। কোনও দেবতা কর্তৃক ‘পাপপূর্ণ’ হিসাবে নিষিদ্ধ করায় নয় বরং এই ধরনের আবেগে আপ্লুত হওয়া মানবীয় প্রকৃতির জন্যে ক্ষতিকর বলে ‘ক্রোধ, অপরাধ, দয়াহীনতা, ঈর্ষা ও লোভের মতো ‘অদক্ষ’ অবস্থা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। সহানুভূতি, সৌজন্য, বিবেচনাবোধ, বন্ধুতা ও দয়া মঠচারী জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো নতুন কৃচ্ছ্রতাবাদ নির্মাণ করেছিল। কিন্তু প্রাচীন, চরম তাপসের বিপরীতে ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য সৃষ্টি করেছে এটা। নিষ্ঠার সঙ্গে বিকাশ সাধিত হলে এটা নিব্বানার সেতো-বিমুত্তি আনতে পারে, আরেক উল্লেখযোগ্য স্বাভাবিক মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা।
কিন্তু কেবল সন্ন্যাসীদের পক্ষেই পূর্ণাঙ্গ ধৰ্ম্ম সম্ভাবপর ছিল। সাধারণ ভারতীয় সংসার জীবনের কোলাহল আর ব্যস্ততা ধ্যান ও যোগসাধনা অসম্ভব করে তুলবে, তো জগত্ত্যাগী কোনও সন্ন্যাসীর পক্ষেই নিব্বানা লাভ সম্ভব। অকাঙ্ক্ষায় পরিচালিত বাণিজ্যিক ও প্রজনন কর্মকাণ্ডে জড়িত অনাথাপিন্দিকার মতো সাধারণ জন লোভ, ঘৃণা ও বিভ্রমের ত্রি-অগ্নি নির্বাপনের আশা করতে পারে না। একজন সাধারণ মানুষ কেবল পরবর্তী জন্মে আলোকনের পক্ষে অনুকূল পরিবেশে পুনর্জন্ম লাভের আশা করতে পারে। মহান সত্যিগুলো আমজনতার জন্যে নয়: ‘এগুলো’ উপলব্ধি করতে হবে আর এই ‘প্রত্যক্ষ জ্ঞান’ বৌদ্ধদের পূর্ণাঙ্গ রীতিনীতি পালনে আবশ্যক যোগ সাধনা ছাড়া অর্জন করা সম্ভব নয়।[৩০] অভিনিবেশের অনুশীলন ছাড়া অনাত্মার মতো মতবাদ কোনও অর্থ বয়ে আনবে না। কিন্তু বুদ্ধ সাধারণ জনকে অগ্রাহ্য করেননি। মনে হয়, দীক্ষা দানের দুটো প্রধান ধারা ছিল: একটা সন্ন্যাসীর জন্যে, অপরটি সাধারণের।
অনাথাপিন্দিকার করুণ মৃত্যুবরণের কাহিনীতে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তিনি মুমূর্ষু হয়ে ওঠার পর সারিপুত্ত ও আনন্দ দেখতে গেলেন তাঁকে। তাঁকে বিদায়ের ওপর ছোট একটা কাহিনী শোনালেন সারিপুত্তঃ অনাথাপিন্দিকাকে ইন্দ্রিয়কে আঁকড়ে না থাকার শিক্ষা নিতে হবে। কারণ বাহ্যিক জগতের সঙ্গে এই সম্পর্ক তাঁকে সামসারার ফাঁদে বন্দি করবে। কেউ একে মৌল বৌদ্ধ শিক্ষা ভাবতে পারেন। কিন্তু অনাথাপিন্দিকা কখনও আগে এমনটি শোনেননি। শুনতে শুনতে গাল বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল তাঁর। ‘ব্যাপার কী, গৃহী? ‘ উদ্বেগের সঙ্গে জানতে চাইলেন আনন্দ। ‘খুব খারাপ লাগছে?’ না, প্রতিবাদ করলেন অনাথাপিন্দিকা, এটা কোনও সমস্যা নয়। ‘গুরু আর ধ্যানী ভিক্ষুদের এত বছর ধরে পরিচর্যা পরিচর্যা করেছি, অথচ আগে কখনও ধম্ম সম্পর্কে এমন কথা শুনিনি।’ এটাই শোকাক্রান্ত করেছে তাঁকে। সাধারণ জনকে এই শিক্ষা দেওয়া হয়নি, ব্যাখ্যা করলেন আনন্দ। কেবল গৃহত্যাগীদের জন্যেই এই শিক্ষা। এটা ঠিক হয়নি, জবাব দিলেন অনাথাপিন্দিকা। গৃহস্থদেরও এইসব বিষয় নির্দেশনা দেওয়া উচিত: এমনও লোকজন রযেছে যাদের মাঝে সামান্য আকাঙ্ক্ষাই অবশিষ্ট আছে। তারা আলোকন লাভের উপযোগি। সুতরাং নিব্বানা লাভ করতে পারবে তারা।[৩১]
সেরাতেই মারা গেলেন অনাথাপিন্দিকা এবং আমাদের জানানো হয়েছে, স্বর্গে একজন ‘স্রোতে প্রবেশকারী’ হিসাবে মাত্র সাতটি পুনর্জন্ম সামনে নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেন তিনি। নিঃসন্দেহে আশীর্বাদ হিসাবে দেখা হয়েছে একে। কিন্তু তাঁর ঔদার্য ও নিবেদিত সেবার বিনিময়ে এই পুরস্কার সামান্য বলে মনে হয়। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এই ধরনের আবিশ্যিক শিক্ষা দূরে সরিয়ে রাখা অন্যায় বোধ হয়। কিন্তু প্রত্যেকের একই আধ্যাত্মিক স্তরে অবস্থানের ধারণাটি আবশ্যিকভাবেই আধুনিক ধারণা। প্রাক-আধুনিক ধর্ম বরাবরই দুটো স্তরে পরিচালিত হতো: অভিজাত একটি গোষ্ঠী সারাজীবন ঐশীগ্রন্থের পাঠ ও ধ্যানে কাটিয়ে দিতেন এবং অনিবার্যভাবে অধিকতর অজ্ঞ সাধারণ জনকে নির্দেশনা দিতেন। সবাই শিক্ষিত ও ধর্মগ্রন্থ পাঠের সুযোগ পাওয়ার পরেই কেবল পূর্ণ ধর্মীয় সাম্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। বিসিই প্রথম শতাব্দীর আগে বৌদ্ধ শাস্ত্র লিপিবদ্ধ করা হয়নি, কিন্তু তরপরেও পাণ্ডুলিপি ছিল বিরল। ধৰ্ম্ম শোনার জন্যে যে কাউকে খোদ বুদ্ধ কিংবা কোনও সন্ন্যাসীর কাছে যেতে হতো।
আমজনতাকে কী শিক্ষা দিয়েছিল সংঘ? একেবারে গোড়া থেকেই বুদ্ধের কাছে ‘আশ্রয় নিয়েছিল’ সাধারণ মানুষ। জনগণ সন্ন্যাসীদের খাইয়ে, সাহায্য করে উন্নত পুনর্জন্মের জন্যে প্রয়োজনীয় পূণ্য অর্জন করত। সন্ন্যাসীগণও সাধারণ মানুষকে নৈতিক জীবন যাপন করে, সৎকর্মের মাধ্যমে কৰ্ম্মকে পরিশুদ্ধ করার শিক্ষা দিতেন যাতে তারা আধ্যাত্মিক অগ্রগতি অর্জন করতে পারে। সবাই একে ন্যায়সঙ্গত বিনিময় হিসাবে দেখেছে। অনাথাপিন্দিকার মতো কোনও কোনও সাধারণ মানুষ বুদ্ধ ও ভিক্ষুদের সঙ্গে প্রচুর সময় কাটিয়েছে। তাদের পাঁচটি নৈতিক শপথ গ্রহণে উৎসাহিত করা হয়েছে– নবীশদের জন্যে ধম্ম: অবশ্যই হত্যা করবে না, চুরি করবে না, মিথ্যা বলবে না বা মাদক সেবন করবে না, অবশ্যই যৌন উচ্ছৃখলতা এড়িয়ে যাবে। মোটামুটি জৈন অনুসারীদের আচরিত অনুশীলনের মতোই ছিল এসব। প্রতি মাসের সপ্তম দিনে (উপসোথা) বৌদ্ধ জনগণের প্রাচীন বৈদিক অনাহার ও নিবৃত্ত থাকার উপবাসতা অনুশীলনের পরিবর্তে বিশেষ উপাচার ছিল; বাস্তবক্ষেত্রে যা তাদের চব্বিশ ঘন্টার জন্যে সংঘের নবীশের মতো কিছুতে পরিণত করেছিল। তারা যৌনতা হতে বিরত থাকত, আমোদ অনুষ্ঠান দেখত না, ভদ্রজনোচিত পোশাক পরত ও মধ্যাহ্ন পর্যন্ত শক্ত খাবার গ্রহণ করত না।[৩২] এটা তাদের পূর্ণাঙ্গ বৌদ্ধ জীবনের একটা স্বাদ যুগিয়েছে, কাউকে কাউকে হয়তো সন্ন্যাসী হতেও অনুপ্রাণিত করেছে।
এমনকি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ধ্যান শুরু করার আগেই যেকোনও যোগির মতো তাঁকে সহানুভূতি, আত্ম-নিয়ন্ত্রণ ও অভিনিবেশের নৈতিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হতো। সাধারণ মানুষ কখনও গভীর যোগ আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়নি, তো তারা নৈতিকতার (শীলা) ওপর জোর দিয়েছে। বুদ্ধ একে তাদের জীবনের উপযোগি করে দিয়েছিলেন। এভাবে সাধারণ নারী-পুরুষ এক পূর্ণাঙ্গ আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি নির্মাণ করছিল যা পরজন্মে তাদের শক্ত অবস্থান গড়ে দেবে। সন্ন্যাসীরা ধ্যানের মাধ্যমে ‘দক্ষ’ কৌশল শিক্ষা করতেন, আর আমজনত্তা ‘দক্ষ’ নৈতিকতার প্রতি জোর দিয়েছে।[৩৩] ভিক্ষুকে দান করা, সবসময় সত্যি কথা বলা ও অন্যদের সঙ্গে দায়ালু ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ তাদের অধিকতর সজীব স্বাস্থ্যবান মানসিক অবস্থা সৃষ্টি ও অহমবাদের আগুন সম্পূর্ণ নিভানো সম্ভব না হলেও কিছুটা প্রশমিত করতে সাহায্য করেছে। এই নৈতিকতার প্রায়োগিক সুবিধা ছিল: এটা অন্যদের তাদের প্রতি একইরকম আচরণে উৎসাহিত করতে পারে। ফল স্বরূপ, পরবর্তী জীবনে পূণ্য অর্জন ছাড়াও বর্তমান জীবনে আরও সুখী হওয়ার উপায় শিক্ষা নিচ্ছিল তারা।
বৈদিক ব্যবস্থায় যাদের কোনও স্থান ছিল না, অনাথাপিন্দিকার মতো ব্যবসায়ী ও মহাজনদের কাছে ধম্ম খুবই আবেদনময় ছিল। চতুর বিনিয়োগ নীতিমালা ভিত্তিক হওয়ায় ব্যবসায়ীরা বুদ্ধের ‘দক্ষ’ নীতিমালা উপলব্ধি করতে পেরেছিল। এটা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অস্তিত্বে সুনাম বয়ে আনবে। সন্ন্যাসীগণ ক্ষণস্থায়ী মানসিক অবস্থার প্রতি মনোযোগি থাকার প্রশিক্ষণ পেয়েছেন: সাধারণ অনুসারীদের আর্থিক ও সামাজিক লেনদেনে আপ্পানদা (মনোযোগ)- এর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৩৪] বুদ্ধ তাদের জরুরি অবস্থার জন্যে সঞ্চয়, নির্ভরশীলদের দেখাশোনা, ভিক্ষুদের সাহায্য করা, ঋণ এড়ানো, পরিবারের জরুরি প্রয়োজন মেটানোর মতো অর্থ সঞ্চয় নিশ্চিত করা ও সতর্কতার সাথে অর্থ বিনিয়োগের জন্যে বলেছেন।[৩৫] মিতব্যয়ী, বিবেচক ও ধীর-স্থির হতে হবে তাদের। সাধারণ মানুষের জন্যে সবচেয়ে উন্নত হিতোপদেশ সিগালা বেদ সুত্তায় সিগালাকে মদ পান, রাত্রি জাগরণ, জুয়া, আলস্য ও অসৎ সঙ্গ এড়ানোর নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।[৩৬] অগ্নি-হিতোপদেশের একটি সাধারণ ভাষ্যে অনুসারীদের তিনটি ‘শুভ-অগ্নি’র পরিচর্যার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। নির্ভরশীলদের যত্ন, স্ত্রী, সন্তান ও ভৃত্যদের দেখাশোনা এবং সংঘের সকল ভিক্ষুকে সহায়তা করতে হবে।[৩৭]
কিন্তু বরাবরের মতো সহনশীলতাই ছিল মুখ্য গুণ। একদিন রাজা পাসেনেদি ও তাঁর স্ত্রী আলোচনাক্রমে সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে, আপন সত্তা ছাড়া তাদের কাছে প্রিয়তম আর কিছু নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি বুদ্ধের সমর্থন না পাবারই কথা। কিন্তু রাজা এই আলাপের কথা জানালে বুদ্ধ তাঁকে ভর্ৎসনা করেননি, অনাত্মার আলোচনায় লিপ্ত হননি বা অষ্টশীল পথের উপর হিতোপদেশ শুরু করেননি। তার বদলে যথারীতি পাসেনেদির দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রবেশ করলেন তিনি এবং তাঁর মনের বিষয়বস্তুর ভিত্তিতেই আলোচনা শুরু করলেন-যেখানে কী থাকা উচিৎ ভেবেছেন তার ভিত্তিতে নয়। সুতরাং, রাজাকে তিনি বলেননি যে, সত্তা একটা বিভ্রম, কারণ নিয়মিত যোগের জীবন ছাড়া তিনি এটা ‘বুঝতে’ পারতেন না। বরং রাজাকে এই বিষয়টি ভাবতে বললেন তিনিঃ তিনি যদি বুঝে থাকেন যে তাঁর কাছে নিজের চেয়ে প্রিয় আর কিছু নেই, তাহলে এটাও নিশ্চয়ই সত্যি যে অপরাপর মানুষও তাদের ‘ভিন্ন সত্তা’ লালন করে। সুতরাং উপসংহার টানলেন বুদ্ধ, ‘যে ব্যক্তি সত্তাকে ভালোবাসে, তার অন্যের সত্তাকে আঘাত দেওয়া উচিৎ নয়।’[৩৮] রেওয়াজ অনুযায়ী যাকে ‘স্বর্ণ বিধি’ বলা হয়, সেটা অনুসরণ করা উচিৎ তাঁর: ‘তুমি নিজের জন্যে যা সঠিক মনে করো না, অন্যের বেলায় তা করো না।[৩৯] সাধারণ মানুষ অহমবাদ পুরোপুরি নির্বাপিত করতে পারে না, কিন্তু অন্য মানুষের দুর্বলতায় সমব্যথী হতে স্বার্থহীনতার অনুভূতি কাজে লাগাতে পারে। এটা অহমের বাড়াবাড়ির ঊর্ধ্বে নিয়ে যাবে তাদের, অহিংসার সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেবে।
আমরা কালামানদের[৪০] উদ্দেশে প্রদত্ত হিতোপদেশে বুদ্ধের সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার কৌশল দেখতে পাই। গাঙ্গেয় উপত্যকার সবচেয়ে উত্তর সীমানায় ছিল এই জাতির বাস। এককালে গোত্রীয় রাজ্য পরিচালনা করলেও এখন কোসালার প্রজায় পরিণত হয়েছে। ক্রমশঃ নতুন শহুরে সভ্যতার অধীনে নিয়ে আসা হচ্ছিল তাদের। এই অভিজ্ঞতা তাদের কাছে অনিশ্চিত ও অপমানকর মনে হয়েছে। বুদ্ধ তাদের কেসাপুত্ত শহর দিয়ে যাওয়ার সময় পরামর্শ চেয়ে এক প্রতিনিধি দল পাঠাল তারা। একের পর এক সাধু আর শিক্ষক তাদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছেন, ব্যাখ্যা করল তারা, কিন্তু প্রত্যেক সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণ যার যার নিজস্ব মতবাদ ব্যাখ্যা করেছেন, অন্যদের অভিশম্পাত করেছেন তাঁরা। এইসব ধম্ম কেবল পরস্পর বিরোধীই নয়, সুসংস্কৃত মূলধারার সংস্কৃতির অংশ বলে অচেনাও ছিল। ‘এইসব শিক্ষকের কে সঠিক, কে ভুল?’ জানতে চাইল তারা। বুদ্ধ বললেন কালামানদের বিভ্রান্ত বোধ করার কারণ বুঝতে পেরেছেন তিনি। যাথারীতি তাদের অবস্থায় প্রবেশ করলেন তিনি। গড়গড় করে নিজ ধম্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাদের বিভ্রান্তি বাড়াননি, মোকাবিলা করার জন্যে নতুন কোনও মতবাদ শোনাননি তাদের, বরং কালামানরা যাতে নিজেরাই সমাধান খুঁজে নিতে পারে, সেজন্যে তাৎক্ষণিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন (সক্রেটিস ও কনফুসিয়াসের মতো অন্যান্য অ্যাক্সিয়াল সাধুদের প্রশ্ন ও উত্তর পদ্ধতির স্মারক)। তিনি এই বলে শুরু করলেন যে, তাদের হতবুদ্ধি হওয়ার অন্যতম কারণ অন্যদের কাছ থেকে জবাব পাওয়ার আশা করছে তারা। কিন্তু যখন নিজেদের হৃদয়ের দিকে চোখ ফেরাবে তখনই বুঝতে পারবে আসলে কোনটা সঠিক।
‘শোন, কালামানবাসী,’ বললেন তিনি। ‘শোনা কথায় সন্তোষ বোধ করো না বা সরল বিশ্বাসে সত্য হিসাবে মেনে নিয়ো না।’ নৈতিকতার প্রশ্নে মানুষকে নিজেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যেমন ধরা যাক, লোভ কি ভালো নাকি খারাপ? ‘খারাপ, প্রভু।’ জবাব দিল কালামানরা। তারা কি লক্ষ করেছে যখন কেউ আকাঙ্ক্ষায় তাড়িত হয়ে কোনও কিছু পেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে তখন হত্যা, চুরি বা মিথ্যার আশ্রয় নিতে পারে সে? হ্যাঁ, কালামনরা এ ব্যাপারটি লক্ষ করেছে। এই ধরনের আচরণ স্বার্থপর মানুষকে কি অজনপ্রিয় ও সেকারণে অসুখী করে না? আর ঘৃণার বেলায়? কিংবা বস্তুকে স্বরূপে দেখার চেষ্টা করার বদলে স্পষ্টতই বিভ্ৰমকে আঁকড়ে থাকা? এইসব আবেগ কি বেদনা আর কষ্টের দিকে চালিত করেনি? ধাপে ধাপে কালমানদের নিজ অভিজ্ঞতা স্মরণ করে লোভ, ঘৃণা আর অজ্ঞতার ‘ত্রি-অগ্নি’র প্রভাব অনুধাবন করতে বললেন তিনি। আলোচনার শেষ নাগাদ কালামানরা বুঝতে পারল, আগে হতেই বুদ্ধের ধম্মের সঙ্গে পরিচিত ওরা। ‘সেজন্যেই আমি তোমাদের কোনও শিক্ষকের ওপর নির্ভর না করতে বলেছি,’ উপসংহার টানলেন বুদ্ধ। ‘তোমরা যখন নিজেরাই কোন জিনিসগুলো ‘সহায়ক’ (কুসলা) আর কোনগুলো ‘অনুপযোগি’ (অকুসলা) বুঝতে পারেব তখন অন্যরা যাই বলুক না কেন তোমরা এই নীতিরই চর্চা করবে ও ধরে রাখবে।’[৪১]
তিনি কালামানদের এও বোঝালেন যে, লোভ, ঘৃণা ও বিভ্রম এড়ানোর পাশাপাশি বিপরীত গুণাবলীর চর্চার করাও নিঃসন্দেহে উপকারী হবে: ‘নির্লোভ, ঘৃণাহীন ও বিভ্রমহীন।’ তারা উপকার, দয়া ও উদারতার বিকাশ ঘটিয়ে জীবন সম্পর্কে যথাযথ উপলব্ধি অর্জনের প্রয়াস পেলে নিজেদের সুখী মানুষ হিসাবে আবিষ্কার করবে। যদি ভিন্ন জীবন আসে (কালামানদের উপর পুনর্জন্মের মতবাদ চাপিয়ে দেননি বুদ্ধ, এর সঙ্গে তাদের পরিচয় নাও থাকতে পারত) তাহলে এই সৎ কন্ট পরবর্তী সময় স্বর্গে দেবতা হিসাবে পুনর্জন্ম দান করবে। অন্য কোনও জগৎ না থাকলে এই সুবিবেচক ও সদয় জীবনধারা অন্যদের নিজেদের প্রতি একই ধরনের আচরণে উৎসাহিত করবে। আর কিছু না হোক, তারা অন্তত এটুকু জানবে যে, সৎ আচরণ করেছে-সেটা সবসময়ই স্বস্তির কারণ হবে। কালামানদের এই ‘দক্ষ’ মানসিকতা গড়ে তোলায় সহায়তা করতে ধ্যানের একটা কৌশল শিক্ষা দিয়েছিলেন বুদ্ধ; এটাই ছিল ‘অপরিমেয়’র সাধারণ মানুষের ভাষ্য। প্রথমে তাদের অবশ্যই মন হতে ঈর্ষা, খারাপ ইচ্ছার অনুভূতি ও বিভ্রম দূর করতে হবে। তারপর সর্বদিকে প্রেমময় দয়ার অনুভূতি প্রেরণ করবে। তখন তারা দেখতে পাবে, ‘প্রচুর মর্যাদাপূর্ণ, অপরিমেয়, প্রেমময়, প্ৰবল দয়ায় পরিপূর্ণ’ হয়ে উঠেছে তারা। তখন তারা নিজেদের সীমিত দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে এসে সমগ্র জগতকে আলিঙ্গন করবে। অহমবাদের তুচ্ছতাকে ছাপিয়ে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে এমন এক মোহাবেশ অনুভব করবে যা তাদের সত্তার বাইরে ‘উর্ধ্বে, নিচে, চারপাশে ও সর্বত্র’ নিয়ে যাবে। তারা দেখবে তাদের হৃদয় নিরাসক্ত প্রশান্তিতে প্রসারিত হয়ে গেছে।[৪২] সাধারণ নারী- পুরুষ নিব্বানার স্থায়িত্ব অর্জন না করতে পারে, কিন্তু চূড়ান্ত মুক্তির আভাস লাভ করতে পারবে।
সুতরাং, বুদ্ধ সন্ন্যাসী ও সাধারণ জনগণকে আগ্রাসি নতুন সমাজে বিরাজিত অহমবাদ প্রশমিত করার জন্যে একই রকম সহানুভূতিপূর্ণ আক্রমণ পরিচালনার শিক্ষা দিচ্ছিলেন। অহমবাদ মানুষকে জীবনের পবিত্র মাত্রা অর্জন হতে দূরে ঠেলে রেখেছিল। তিনি যে দক্ষ অবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তা পালি লিপির এই কবিতায় চমৎকার ফুটে উঠেছে:
সকল প্রাণী সুখী হোক! শক্তিশালী কি দুর্বল, উচ্চ, মধ্য
বা নিচু গোত্রের,
ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, দৃশ্য বা অদৃশ্য, কাছের বা দূরের,
জীবিত বা জন্ম প্রত্যাশী-সকলেই সুখী হোক!
কেউ যেন কাউকে মিথ্যা না বলে বা কোথাও কোনও সত্তাকে
ঘৃণা না করে।
কেউ যেন ক্রোধ
বা ঘৃণা বশত কোনও প্রাণীর অমঙ্গল কামনা না করে!
আসুন সকল প্রাণীর লালন করি, মা যেমন তার সন্তানকে লালন করে।
আমাদের প্রেমময় চিন্তা যেন ঊর্ধ্ব-অধের গোটা পৃথিবীকে পরিপূর্ণ করে
সীমাহীনভাবে; এক সীমাহীন শুভেচ্ছা গোটা জগতের প্রতি,
ঘৃণা ও শত্রুতা হতে মুক্ত, বাধাহীন![৪৩]
এই প্রবণতা অর্জনকারী সাধারণ মানুষ আধ্যাত্মিক পথে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে।
ধর্মগ্রন্থসমূহ সংঘের বাইরে ধ্যানের চর্চা করে নিব্বানা লাভকারী সাধারণ শিক্ষাব্রতী সম্পর্কে গুটিকয় নজীর তুলে ধরে, তবে নিঃসঙ্গ অলোকসামান্য ব্যক্তিগণ নিয়ম নন বরং ব্যতিক্রম ছিলেন। মনে করা হতো যে, কোনও আরাহান্তের পক্ষে সংসার জীবন অব্যাহত রাখা সম্ভব নয়: আলোকপ্রাপ্ত হওয়ার পরই হয় তিনি সংঘে যোগ দেবেন বা মারা যাবেন। দৃশ্যতঃ বুদ্ধের বাবা শুদ্ধোদনের বেলায় এমনটাই ঘটেছিল, ছেলের দীক্ষা দানের পঞ্চম বছরে নিব্বানা অর্জন করেন তিনি এবং পরদিনই মারা যান। বুদ্ধ এই সংবাদ পেয়ে কাপিলবাস্তুতে ফিরে কিছুদিন নিগরোধা উদ্যানে অবস্থান করেছিলেন। এই ঘটনা সংঘের নতুন পরিবর্তন বয়ে এনেছিল, বুদ্ধ প্রথমে যাকে ভালোভাবে নেননি বলেই মনে হয়।
তিনি নিগরোধ আরামায় অবস্থান করার সময় বাবার বিধবা স্ত্রী ও বুদ্ধের খালা পজাপতি গৌতমী তাঁর কাছে আসেন। আপন মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর পালক মায়ে পরিণত হয়েছিলেন তিনি। যেহেতু এখন তিনি মুক্ত, বোনের ছেলেকে বলেন তিনি, তাই সংঘে যোগ দিতে চান। জোরের সাথে প্রত্যাখ্যান করলেন বুদ্ধ। সংগঠনে মহিলাদের গ্রহণ করার প্রশ্নই ওঠে না। এমনকি পজাপতি তিনবার বিবেচনার আবেদন জানানো সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত পাল্টাবেন না তিনি। খুবই দুঃখের সঙ্গে বিদায় নিলেন পজাপতি। কয়েকদিন পর গঙ্গার উত্তর তীরবর্তী বিদেহা প্রজাতন্ত্রের রাজধানী বেসালির উদ্দেশে রওনা হলেন বুদ্ধ। প্রায়শঃই সেখানকার আরামায় অবস্থান করতেন তিনি। উঁচু ছাদঅলা একটা মিলানায়তন ছিল এখানে। বারান্দায় অন্যান্য শাক্য মহিলাদের সঙ্গে পজাপতিকে কাঁদতে দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠলেন আনন্দ। চুল কেটে ফেলেছেন মহিলা, গায়ে গেরুয়া বসন চাপিয়ে সেই কাপিলাবাস্তু থেকে পায়ে হেঁটে এসেছেন এত দূর। পা ফুলে গিয়েছিল তাঁর, ধূলিমলিন, পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ‘গৌতমী,’ চেঁচিয়ে উঠলেন আনন্দ; ‘এখানে এই হালে কী করছেন আপনি? কাঁদছেনই বা কেন?’ ‘কারণ আশীবার্দপ্রাপ্ত জন সংঘে মেয়েদের যোগ দিতে দেবেন না।’ জবাব দিলেন পজাপতি। উদ্বিগ্ন বোধ করলেন আনন্দ। ‘এখানে অপেক্ষা করুন,’ বললেন তিনি। ‘এব্যাপারে তথাগতকে জিজ্ঞেস করছি আমি।’
কিন্তু তারপরও ব্যাপারটা বিবেচনা করতে অস্বীকার গেলেন বুদ্ধ। গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত এটা। নারীদের সংঘের বাইরে রাখা অব্যাহত রাখলে তার মানে দাঁড়াত মানবজাতির অর্ধেক অংশকে আলোকপ্রাপ্তির অযোগ্য মনে করছেন তিনি। কিন্তু ধম্ম সবার হওয়ার কথা: দেবতা, পশুপাখি, ডাকাত, সকল গোত্রের মানুষ–কেবল নারীরাই বাদ পড়বে? কেবল পুরুষ হিসাবে পুনর্জন্মই তাদের সবচেয়ে ভালো আশা হবে? অন্যভাবে চেষ্টা করলেন আনন্দ। ‘প্রভু,’ জিজ্ঞেস করলেন তিনি, ‘নারীরা “স্রোতে প্রবেশকারী” হয়ে শেষ পর্যন্ত আরাহান্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখে?’ ‘রাখে, আনন্দ,’ জবাব দিলেন বুদ্ধ। ‘তাহলে পজাপতিকে বরণ করে নেওয়াই মঙ্গলজনক হবে,’ আবেদন জানালেন আনন্দ। মায়ের মৃত্যুর পর মহিলার আদর যত্নের কথা মনে করিয়ে দিলেন তিনি গুরুকে। অনীহার সঙ্গে পরাজয় মেনে নিলেন বুদ্ধ। আটটি কঠিন নিয়ম মেনে নিলেই কেবল সংঘে প্রবেশ করতে পারবেন পজাপতি। এই বিধানগুলো এটা পরিষ্কার করে নিয়েছে যে নানরা (ভিক্ষুনি) নিম্ন পর্যায়ের গোত্র। অল্পবয়সী বা নব্য দীক্ষিত হলেও পুরুষ ভিক্ষুর উপস্থিতিতে ভিক্ষুনিকে অবশ্যই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে; নানদের সবসময় বাস্যার অবকাশ কোনও আরামায় একাকী নয় বরং পুরুষ সন্ন্যাসীদের সঙ্গে কাটাতে হবে; পাক্ষিক একবার একজন পুরুষ ভিক্ষুর কাছে সবক নিতে হবে; নিজেরা কোনও শাস্ত্রাচার করতে পারবে না; গুরুতর অন্যায়কারী পাপীকে ভিক্ষুনি ও সন্ন্যাসীদের উপস্থিতিতে প্রায়শ্চিত করতে হবে; একজন ভিক্ষুনিকে অবশ্যই পুরুষ ও নারী উভয় সংঘের কাছে যাজকানুষ্ঠানের অনুরোধ জানাতে হবে; সে কখনও কোনও ভিক্ষুকে বকাঝকা করতে পারবে না, যদিও যেকোনও সন্ন্যাসী তাকে ভর্ৎসনা করতে পারবে; ভিক্ষুদের শিক্ষাও দিতে পারবে না সে। সানন্দে এইসব বিধান মেনে নিলেন পজাপতি। বরণ করে নেওয়া হলো তাঁকে। কিন্তু তারপরও অস্বস্তিতে ভুগছিলেন বুদ্ধ। মহিলাদের যোগ দিতে না দেওয়া হলে, আনন্দকে বললেন তিনি, ধম্ম হয়তো হাজার বছর ধরে পালিত হতো। এখন বড় জোর পাঁচ শো বছর টিকে থাকবে। অসংখ্য নারী বিশিষ্ট গোত্র দুর্বল হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে; একইভাবে নারী সদস্যঅলা কোনও সংঘ বেশিদিন টিকতে পারে না। ধান ক্ষেতে ছত্রাকের মতো সংগঠনের ওপর ছড়িয়ে পড়বে তারা।[৪৪]
এই নারী বিদ্বেষ হতে কী বুঝতে পারি আমরা? বুদ্ধ সবসময়ই নারী ও পুরুষ উভয়কে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি অনুমতি দেওয়ার পর হাজার হাজার নারী ভিক্ষুনিতে পরিণত হয়েছে। তাদের আধ্যাত্মিক অর্জনের প্রশংসা করেছেন বুদ্ধ। বলেছেন তারা সন্ন্যাসীদের সমপর্যায়ের হতে পারে। যথেষ্ট প্রাজ্ঞ সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুনি, সাধারণ পুরুষ ও সাধারণ নারী অনুসারী না সংগ্রহ করা পর্যন্ত পরলোকে না যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।[৪৫] টেক্সটে কোনও রকম বৈসাদৃশ্য আছে বলে মনে হয়। এটা কোনও কোনও পণ্ডিতকে এই উপসংহারে পৌঁছতে তাড়িত করেছে যে, নারীদের গ্রহণ করার বেলায় ক্রুদ্ধ সম্মতির কাহিনী ও আটটি বিধান পরবর্তী সময়ে সংযোজন, তা সংগঠনের পুরুষতান্ত্রিকতাকে প্রতিফলিত করে। বিসিই প্রথম শতাব্দী নাগাদ সন্ন্যাসীদের কেউ কেউ অবশ্যই তাঁদের আলোকপ্রাপ্তি হতে দূরে ঠেলে রাখা যৌনাকাঙ্ক্ষার জন্যে নারীদের দায়ী করেছেন। নারীদের তাঁরা আধ্যাত্মিক অগ্রগতির পথে সর্বজনীন বাধা হিসাবে দেখেছেন। অন্য পণ্ডিতগণ যুক্তি দেখিয়েছেন যে, আলোকপ্রাপ্ত হলেও বুদ্ধ সেই সময়ের সামাজিক শর্তাবলী এড়িয়ে যেতে পারেননি। পিতৃতান্ত্রিক নয়, এমন সমাজ কল্পনা করতে পারেননি তিনি। তাঁরা যুক্তি তুলে ধরেছেন, বুদ্ধের প্রাথমিক অনীহা সত্ত্বেও নারীদের অন্তর্ভুক্তি ব্যতিক্রমী কাজ ছিল যা প্রথমবারের মতো নারীদের সংসারের বাইরে একটা বিকল্পের সন্ধান দিয়েছিল।[৪৬]
একথা সত্যি হলেও নারীদের জন্যে সমস্যা ছিল যা উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। বুদ্ধের মনে নারীরা হয়তো আলোকনকে অসম্ভব করে তোলা ‘কামনা’ হতে অবিচ্ছেদ্য ছিল। বাড়ি ছেড়ে সন্ধানে নামার সময় কোনও কোনও গৃহত্যাগীর মতো স্ত্রীকে সঙ্গী করার কথা ভাবেননি তিনি। স্রেফ ধরে নিয়েছিলেন তিনি (স্ত্রী) মুক্তি লাভে সঙ্গী হতে পারবেন না। কিন্তু সেটা গীর্জার ক্রিশ্চান ফাদারদের মতো যৌনতাকে বিরক্তিকর ভেবেছিলেন বলে নয়, বরং স্ত্রীর প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন তিনি। ধর্মগ্রন্থে একটি অনুচ্ছেদ রয়েছে যা সন্ন্যাসীদের প্রক্ষেপণ বলে পণ্ডিতগণ একমত। ‘প্রভু, আমরা নারীদের সঙ্গে কেমন আচরণ করব?’ জীবনের শেষ দিকে বুদ্ধকে জিজ্ঞেস করলেন আনন্দ। ‘ওদের দিকে তাকিয়ো না, আনন্দ।’ ‘ওদের দিকে না তাকালে কেমন করে আচরণ করব?’ ‘ওদের সঙ্গে কথা বলো না, আনন্দ।’ ‘কিন্তু যদি কথা বলতে হয়?’ ‘অবশ্যই অভিনিবেশ পালন করতে হবে, আনন্দ।’[৪৭] বুদ্ধ ব্যক্তিগতভাবে হয়তো নারী বিদ্বেষ সমর্থন করতেন না, কিন্তু এমন হতে পারে যে এই কথাগুলো তিনি অতিক্রম করতে পারেননি এমন অস্বস্তির অবশেষ।
বুদ্ধ নারীদের ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে থাকলে সেটা অ্যাক্সিয়াল যুগেরই রেওয়াজ। দুঃখজনক যে, সভ্যতা নারীর প্রতি সদয় ছিল না। প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারসমূহ দেখায়, প্রাক-শহুরে সমাজে কখনও কখনও নারী উচ্চ মর্যাদা পেয়েছে, কিন্তু সামরিক রাষ্ট্রের উত্থান ও আদি নগরসমূহে বিশেষায়ণ তাদের অবস্থানের অবনতি ঘটিয়েছে। পুরুষ মানুষের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে তারা, প্রায় সব পেশা হতে বাদ পড়েছে এবং মাঝে মাঝে প্রাচীন কোনও আইনি বিধানের কারণে নিষ্ঠুর নিয়ন্ত্রণের শিকার হয়েছে। অভিজাত নারীগণ কিছুটা ক্ষমতা ধরে রাখতে পেরেছেন, বুদ্ধ যখন ভারতে ধর্ম প্রচারণা করছেন, তখন অ্যাক্সিয়াল দেশসমূহে নারীরা আরও মর্যাদা হারিয়েছে। ইরান, ইরাক ও পরবর্তীকালে হেলেনিস্টিক দেশসমূহে মহিলাদের পর্দার আড়ালে হেরেমে বন্দি করা হয়েছে। নারী বিদ্বেষী ধ্যান-ধারণা বিকাশ লাভ করেছে। ধ্রুপদী এথেন্সের (৫০০-৩২৩) নারীরা বিশেষভাবে সুবিধা বঞ্চিত এবং সমাজ হতে প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিল। কথিত আছে, নীরবতা ও আত্মসমর্পণই ছিল তাদের প্রধান গুণ। আদি হিব্রু ট্র্যাডিশনসমূহ মিরিয়িাম, ডেবোরাহ্ ও জায়েলের মতো নারীদের কাহিনীকে মর্যাদা দিয়েছে, কিন্তু বিশ্বাসের পয়গম্বরীয় সংস্কারের পর ইহুদি আইনে তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীতে অবনমিত করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য, মিশরের মতো দেশে, যা কিনা প্রাথমিকভাবে অ্যাক্সিয়াল যুগে অংশ নেয়নি, নারীদের প্রতি অধিকতর উদার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল।[৪৮] মনে হয়, নতুন আধ্যাত্মিকতার নারীদের প্রতি এক ধরনের অন্তর্গত বৈরিতা ছিল যা আমাদের সময় পর্যন্ত অব্যহত রয়ে গেছে। বুদ্ধের অন্বেষণ বীরত্বের দিক থেকে পুরুষালি: সব বাধা দূর করার প্রতিজ্ঞা, গৃহস্থ জগৎ ও নারীদের প্রত্যাখ্যান, নিঃসঙ্গ সংগ্রাম ও নতুন জগতে প্রবেশ, সমস্তই পুরুষালি গুণের প্রতাঁকে পরিণত হয়েছে। কেবল আধুনিক যুগে ক্রমেই এই প্রবণতার পরিবর্তন ঘটেছে। নারী তার নিজস্ব ‘যুক্তি’ খুঁজে নিয়েছে (এমনকি বুদ্ধের মতো একই শব্দ ব্যবহার করেছে তারা)। তারাও পুরোনো কৰ্তৃত্ব অস্বীকার করেছে এবং নিজস্ব নিঃসঙ্গ যাত্রায় নেমেছে।
নারীরা সংগঠনকে ধ্বংস করবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন বুদ্ধু, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সংঘে প্রধান সংকট দেখা দিয়েছিল পুরুষ অহমের সংঘাতের কারণে।[৪৯] বৌদ্ধ নীতিমালা অনুযায়ী অন্যায়কারী ভুল না বোঝা পর্যন্ত কোনও অপরাধ শাস্তিযোগ্য নয়। কোসাম্বিতে একজন আন্তরিক ও জ্ঞানী সাধুঁকে বহিষ্কার করা হয়। এই শাস্তিকে অন্যায় বলে প্রতিবাদ করেন তিনি, যেহেতু অন্যায় করার বিষয়টি তিনি বুঝতে পারেননি। কোসাম্বির ভিক্ষুরা নিমেষে বৈরী উপদলে ভাগ হয়ে যায়। বুদ্ধ এই বিভেদে এমনই বিপর্যস্ত বোধ করেছিলেন যে এক পর্যায়ে একাকী বনে বাস করতে চলে যান তিনি, আগ্রাসী সঙ্গীদের কাছে নাস্তানাবুদ এক হাতির সঙ্গে সখ্য গড়ে তোলেন। ঘৃণা, বলেছেন বুদ্ধ, কখনও আরও ঘৃণায় হ্রাস পায় না। কেবল বন্ধুত্ব ও সহানুভূতি দিয়েই তা নাকচ করা সম্ভব।[৫০] তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, উভয় দলই ন্যায়ের পক্ষে আছে; কিন্তু বুদ্ধ এক পক্ষকে অন্য পক্ষের অবস্থান বোঝানোর চেষ্টা সত্ত্বেও সকল ভিক্ষুর অহমবাদ অপর পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা অসম্ভব করে তুলেছিল। সারিপুত্ত ও নারীদের সংঘের প্রধান পজাপতিকে তিনি তিনি দু’পক্ষকেই সম্মানের সঙ্গে দেখাতে বলেছেন। উভয় শিবিরকে নিরপেক্ষভাবে দান করার নির্দেশ দিয়েছেন অনাথাপিন্দিকাকে। কিন্তু কোনও সমাধান চাপিয়ে দেননি তিনি। খোদ অংশগ্রহণকারীদের ভেতর থেকেই সমধান আসতে হবে। শেষ পর্যন্ত বরখাস্ত ভিক্ষু শান্ত হলেন: যদিও সেটা তার জানা ছিল না, কিন্তু তিনি অপরাধ করেছেন। অবিলম্বে পুনর্বহাল করা হলো তাঁকে এবং বিবাদের পরিসমাপ্তি ঘটল।[৫১]
এই কাহিনী আমাদের আদি সংঘ সম্পর্কে অনেক কিছু জানায়। সুসংহত সংগঠন ও কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব বলে কিছু ছিল না। প্রাচীন রাজ্যগুলোর সংঘের কাছাকাছি ছিল তা, যেখানে পরিষদের সকল সদস্যের মর্যাদা ছিল সমান। বুদ্ধ কর্তৃত্বপরায়ণ ও নিয়ন্ত্রক শাসক হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। পরবর্তী কালের ক্রিশ্চান ধর্মীয় সংস্থার ফাদার সুপিরিয়রের মতো ছিলেন না তিনি। আসলে একে একটি সংগঠন বলা ঠিক হবে না, বরং বিভিন্ন ধরনের সংগঠন একই ধৰ্ম্ম অনুসরণ করত ও একই জীবনধারা অনুযায়ী চলত। ছয় বছর পর পর বিক্ষিপ্ত ভিক্ষু ও ভিক্ষুনিরা ‘পতিমোক্ষ’ (‘শপথ’) নামে পরিচিত বিশ্বাসের ঘোষণা দিতে সমবেত হতেন।[৫২] নামটা যেমন বোঝায়, সংঘকে এক সূত্রে গাথাই ছিল এর উদ্দেশ্য:
ক্ষতিকর সমস্ত কিছু হতে বিরত থেকো
যা কিছু দক্ষ তা অর্জন করো
মনকে পরিশুদ্ধ করো,
এটাই বুদ্ধের শিক্ষা।
আত্ম সংযম ও ধৈর্য সমস্ত কৃচ্ছ্রতার
মাঝে সেরা,
বুদ্ধ ঘোষণা দিয়েছেন যে নিব্বানাই
সর্বোত্তম মূল্য,
অপরকে যে আঘাত করেনি সেই সত্যিকার
অর্থে গৃহস্থ জীবন হতে ‘অগ্রসর’ হতে পেরেছে।
অপরকে যে আহত করে না সে-ই প্রকৃত সন্ন্যাসী।
ছিদ্রান্বেষণ নয়, নয় ক্ষতি, নয় সংযম,
খাদ্য, একক শয্যা ও আসন সম্পর্কে জানা
ধ্যান হতে প্রাপ্ত উচ্চতর অনুভূতি প্রয়োগ,
জাগ্রত জন এই শিক্ষাই দিয়েছেন।[৫৩]
প্রজাতন্ত্রগুলোর বৈশিষ্ট্য পূর্ণ সম্মেলনের অনুরূপ এই অনুষ্ঠানের প্রতি বেশ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন বুদ্ধ। কাউকেই পতিমোক্ষ থেকে অনুপস্থিত থাকার সুযোগ দেওয়া হতো না, কারণ কেবল এই বিষয়টি আদি সংঘকে একত্রিত রেখেছিল।
অনেক পরে, বুদ্ধের পরলোকগমনের পর, সহজ আবৃত্তিকে আরও বিস্ত ারিত জটিল সম্মেলন দিয়ে পুনস্থাপিত করা হয়। প্রত্যেক অঞ্চলে পাক্ষিক ভিত্তিতে স্থানীয় সম্প্রদায় উপসোথা দিবসে এর আয়োজন করে। এই পরিবর্তন সংঘের একটি গোত্র হতে সংঘে পরিবর্তন তুলে ধরে। অন্য গোত্র থেকে পৃথককারী ধম্ম না গেয়ে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসীনিরা সংঘের বিধিবিধান আবৃত্তি করতেন ও পরস্পরের কাছে অধিকার লঙ্ঘনের দায় স্বীকার করতেন। ততদিনে সংঘের বিধানের সংখ্যা বুদ্ধের আমলের তুলনায় অনেক বেড়ে গিয়েছিল। কোনও কোনও পণ্ডিত যুক্তি দেখান যে, বিনয়ায় লিপিবদ্ধ নিয়ম কানুন চূড়ান্ত রূপ নিতে দুই থেকে তিন শতাব্দী সময় লেগেছে। কিন্তু কেউ কেউ বিশ্বাস করেন, সংগঠনের চেতনা অন্ততপক্ষে মোটামুটিভাবে খোদ বুদ্ধ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া সম্ভব।[৫৪]
সংঘই বৌদ্ধ মতবাদের প্রাণ, কারণ এর জীবনধারা বাহ্যিকভাবে নিব্বানার অন্তস্থ অবস্থা ধারণ করে।[৫৫] সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসীনিদের অবশ্যই কেবল গৃহ হতেই ‘অগ্রসর হতে’ হবে না বরং সত্তাও ত্যাগ করতে হবে। একজন ভিক্ষু ও ভিক্ষুনি প্রাপ্তি ও ব্যয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত ‘আকাঙ্ক্ষা’ বিসর্জন দিয়েছেন, তাদের যা দেওয়া হয় সম্পূর্ণ তার উপর নির্ভর করেন তাঁরা। সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকেন। সংঘের জীবনধারা সদ্যস্যদের ধ্যানে সাহায্য করে আমাদের দুঃখ-কষ্টের চাকায় বেঁধে রাখা অজ্ঞতা, লোভ ও ঘৃণার আগুন দূর করতে সক্ষম করে তোলে। সহানুভূতি ও সাম্প্রদায়িক ভালোবাসার আদর্শ নিজস্ব অহমবাদ একপাশে সরিয়ে রেখে অন্যের জন্যে বাঁচতে শেখায়। এইসব প্রবণতাকে অভ্যাসে পরিণত করে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসীনিরা অটল অন্তস্থ শান্তি –পবিত্র জীবনের মোক্ষ-নিব্বানা অর্জন করতে পারে। সংঘ পৃথিবীর বুকে এখনও টিকে থাকা অন্যতম প্রাচীন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। একমাত্র জৈন সংগঠনই এমনি প্রাচীনত্ব দাবি করতে পারে। এর স্থায়িত্ব মানুষ ও মানবীয় জীবন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু জানায় আমাদের। সুবিশাল সৈন্যবাহিনী দিয়ে পারিচালিত বিরাট বিরাট রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। কিন্তু ভিক্ষুদের সংগঠন প্রায় ২,৫০০ বছর টিকে আছে। আদি বুদ্ধ কিংবদন্তীতে বুদ্ধ ও চক্কবত্তীকে পাশাপাশি দেখিয়ে যে বৈপরীত্যের আভাস দেওয়া হয়েছিল: এটা তাই। বার্তাটিকে এমন মনে হয় যে, নিজেকে রক্ষা করে নয়, বরং নিজেকে বিলিয়ে দিয়েই আপনি বেঁচে থাকতে পারেন।
কিন্তু সংঘের সদস্যরা সিংহভাগ জনগণের জীবনধারার দিকে পিঠ ফিরিয়ে নিলেও সাধারণভাবে লোকে কিন্তু তাঁদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়নি, বরং তাঁদের দারুণভাবে আকর্ষণীয় মনে করেছে। এটাও আমাদের জানায় যে বুদ্ধের আবিষ্কৃত জীবন পদ্ধতি অমানবিক মনে করা হয়নি, বরং গভীরভাব মানবিক আরামাগুলো নির্জন আউটপোস্ট ছিল নাঃ রাজণ্য, ব্রাহ্মণ, বণিক, ব্যবসায়ী, আমাত্য, অভিজাত এবং অন্যান্য গোত্রের সদস্যরা ভিড় জমাতেন এখানে। পাসেনেদি ও বিম্বিসারা নিয়মিত বুদ্ধের পরামর্শের জন্যে আসতেন। বুদ্ধ হয়তো অপরাহ্নে পদ্মপুকুরের ধারে বসে থাকতেন, কিংবা কুঁড়ে ঘরের বারান্দায় বসে মোমবাতির শিখায় মথের ঝাঁপিয়ে পড়া দেখতেন। বুদ্ধ বসতিগুলোয় সাধুদের ভিড় জমানোর কথা পড়ি আমরা। বুদ্ধকে প্রশ্ন করতে প্রতিনিধি দল আসত। হাতির পিঠে চেপে অভিজাতজন ও বণিকরা আসতেন এবং কোনও অঞ্চলের তরুণের দল বুদ্ধকে খাবার আমন্ত্রণ জানাতে সদলবলে হাজির হতো।
এমনি উত্তেজনা ও কর্ম চাঞ্চল্যের ভেতর থাকতেন বুদ্ধের শান্ত নিয়ন্ত্রিত অবয়ব, নতুন ‘জাগ্রত’ পুরুষ। আমাদের মধ্যে যারা তাঁর মতো সম্পূর্ণ আত্ম- পরিত্যাগে অক্ষম তাদের কাছে তিনি অস্পষ্ট ও জ্ঞানাতীত রয়ে যান, কারণ আলোকপ্রাপ্তির পর নৈর্ব্যক্তিক হয়ে গেছেন তিনি, যদিও কখনওই দয়াহীন বা শীতল নন। তাঁর দিক হতে সংগ্রাম বা প্রয়োসের কোনও চিহ্ন নেই। আলোকপ্রাপ্তির রাতে যেমন চেঁচিয়ে উঠেছিলেন, যা করার তার সবই সম্পন্ন করেছেন তিনি। তিনি তথাগত, যিনি অদৃশ্য হয়ে গেছেন। তাঁর কোনও ব্যক্তিগত বন্ধন ছিল না; ছিল না কোনও আগ্রাসী তাত্ত্বিক মতবাদও। পালি টেক্সটে প্রায়শঃ তাঁকে অমানবীয় সত্তার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, সেটা তাঁকে অতিপ্রাকৃত মনে করা হয়েছে বলে নয়, বরং মানুষ তাঁকে কোন শ্রেণীতে ফেলতে হবে জানত না বলে। এক ব্রাহ্মণ একদিন দেখলেন, একটা গাছের নিচে স্থির, ধ্যানমগ্ন বুদ্ধ বসে আছেন। ‘তাঁর মানসিক শক্তি বিশ্রামরত, তাঁর মন অটল। তাঁর আশপাশের সবকিছু আত্মনিয়ন্ত্রণ ও প্রশান্তি প্রকাশ করছিল।’ এ দৃশ্য ব্রাহ্মণকে বিস্ময়াভিভূত করে তুলল। বুদ্ধকে দেখে দাঁতাল হাতির কথা মনে হলো তাঁর: অপরিমেয় শক্তি ও বিপুল সম্বাবনাকে নিয়ন্ত্রণে এনে বিরাট শান্তিতে পরিণত করার সেই একই ছবি। শৃঙ্খলা, সংযম ও পরিপূর্ণ প্রশান্তি বিরাজ করছিল। এমন মানুষ কখনও দেখেননি ব্রাহ্মণ। ‘আপনি কি দেবতা, প্রভু?’ জিজ্ঞেস করলেন তিনি। ‘না,’ জবাব দিলেন বুদ্ধ। ‘আপনি কি তবে দেবদূত…বা আত্মায় রূপান্তরিত হচ্ছেন?’ আবার প্রশ্ন করলেন ব্ৰাহ্মণ। কিন্তু বুদ্ধ আবার জবাব দিলেন, তিনি তা নন। ভিন্ন কিছুতে রূপান্তরিত হয়েছিলেন তিনি। হাজার হাজার বছর আগে পৃথিবীতে জীবন কাটানো শেষ বুদ্ধের পর তাঁর মতো মানুষ জগৎ আর দেখেনি। বিগত এক জীবনে একবার দেবতা ছিলেন তিনি, ব্যাখ্যা দিয়েছেন বুদ্ধ; পশু ও সাধারণ মানুষ হিসাবেও জীবন কাটিয়েছেন, কিন্তু প্রাচীন, অসজীব মানবতার সঙ্গে তাঁকে বন্দি করে রাখা সবকিছু নির্বাপিত হয়ে গেছে, ‘একেবারে গোড়ায় কাটা পড়েছে, তাল গাছের গুঁড়ির মতো উপড়ে ফেলা হয়েছে, সম্পূর্ণ উৎপাটিত।’ ব্রাহ্মণ কি কখনও এমন লাল পদ্ম দেখেছেন যেটা জলের গভীরে জীবন শুরু করে জল ছাড়িয়ে না যাওয়া পর্যন্ত পুকুরের ওপর উঠে এসেছে? জিজ্ঞেস করলেন বুদ্ধ। আমিও পৃথিবীতে জন্ম নিয়ে বড় হয়েছি,’ অতিথিকে বললেন তিনি। ‘কিন্তু আমি জগৎ ছাড়িয়ে গেছি। এখন আর এর সংস্পর্শে নেই।’ এই জীবনে নিব্বানা লাভের মাধ্যমে মানুষের প্রকৃতিতে এক নতুন সম্ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন তিনি। বেদনার এই জগতে অবশিষ্ট সৃষ্টির সঙ্গে শান্তিতে, নিজের সঙ্গে সুনিয়ন্ত্রিত ও সামঞ্জস্যের সঙ্গে বাঁচা সম্ভব। কিন্তু এই শান্ত নিষ্কৃতি লাভের জন্যে নারী- পুরুষকে অহমবাদ হতে বেরিয়ে এসে সম্পূর্ণ অন্যান্য সত্তার স্বার্থে জীবন যাপন করতে হবে। বহিরাগত কারও কাছে যত ভীতিকরই মনে হোক না কেন সত্তার কাছে এমন মৃত্যু-অন্ধকার নয়। এটা মানুষকে তার নিজস্ব প্রকৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ করে তোলে যাতে তারা নিজেদের ক্ষমতার সর্বোচ্চ বিন্দুতে বাস করতে পারে। বুদ্ধকে কেমন করে শ্রেণীবন্ধ করবেন ব্রাহ্মণ? ‘আমার কথা মনে রেখ,’ তাঁকে বলেছেন বুদ্ধ, ‘জাগ্রত একজন হিসাব।[৫৬]
তথ্যসূত্র
১. সাম্যত্তা নিকয়া, ২২: ৮৭।
২. অ্যান্ড্রু স্কিলটন, আ কনসাইজ হিস্ট্রি অভ বুদ্ধজম, বার্মিংহাম, যুক্তরাজ্য, ১৯৯৪, ১৯।
৩. বিনয়া: কুলাভাগ্য, ১: ১২; সুকুমার দত্ত, বুড্ডিস্ট মঙ্কস অ্যান্ড মনাস্টারিজ অভ ইন্ডিয়া, লন্ডন, ১৯৬২, ২২।
৫. বিনয়া: মহাভাগ্য, ১: ১৩।
৬. প্রাগুক্ত, ১: ১৪-২০।
৭. মির্চা এলিয়াদ, ইয়োগা, ইমমর্টালিটি অ্যান্ড ফ্রিডম (অনু. উইলিয়াম আর, ট্রাস্ক); লন্ডন, ১৯৫৮, ৮৫-৯০।
৮. সুত্তা নিপাতা, ১৩৬; উদনা, ১: ৪।
৯. বিনয়া: মহাভাগ্য, ১: ২০।
১০. প্রাগুক্ত, ১: ২১; সাম্যত্তা নিকয়া, ৩৫: ২৮।
১১. রিচার্ড এফ. গমব্রিচ; থেরাভেদা বুদ্ধজম: আ সোশ্যাল হিস্ট্রি ফ্রম অ্যানশেন্ট বেনারেস টু মডার্ন কলোম্বো, লন্ডন ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৮, ৬৫-৬৯।
১২. বিনয়া: মহাভাগ্য, ১: ২১।
১৩. প্রাগুক্ত, ১: ২২।
১৪. প্রাগুক্ত, ১: ২৩।
১৫.এডোয়ার্ড কনযে, বুদ্ধজম; ইটস্ এসেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, অক্সফোর্ড ১৯৫৭, ৯১-৯২।
১৬. বিনয়া: মহাভাগ্য, ১: ২৪।
১৭. জাতকা, ১: ৮৭; আঙুত্তারা নিকয়ার ব্যাখ্যা, ১: ৩০২; এডোয়ার্ড জে. টমাস. দ্য লাইফ অভ বুদ্ধা ইন লেজেন্ড অ্যান্ড হিস্ট্রি, লন্ডন, ১৯৬৯, ৯৭- ১০২; ভিক্ষু নানামোলি (অনু. ও সম্পা.), দ্য লাইফ অভ দ্য বুদ্ধা, অ্যাকর্ডিং টু দ্য পালি ক্যানন, ক্যান্ডি, ক্যান্ডি, শ্রী লঙ্কা, ১৯৭২, ৭৫-৭৭।
১৮. টমাস, লাইফ অভ বুদ্ধা, ১০২-৩
১৯. বিনয়া কুলাভাগ্য, ৬: ৪; সাম্যত্তা নিকয়া, ১০: ৮।
২০. ট্রেভর লিঙ, দ্য বুদ্ধা: বুড্ডিস্ট সিভিলাইজেশন ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড সিলোন, লন্ডন, ১৯৭৩, ৪৬-৪৭।
২১. বিনয়া: কুলাভাগ্য, ৬: ৪; সাম্যত্তা নিকয়া ১০: ৮।
২২. দত্ত, বুড্ডিস্ট মঙ্কস, ৫৮।
২৩. বিনয়া: মহাভাগ্য, ৩: ১।
২৪. প্রাগুক্ত, ৮: ২৭।
২৫. বিনয়া: কুলাভাগ্য, ৬: ৫-৯।
২৬. মাজহিমা নিকয়া, ১২৮; বিনয়া: মহাভাগ্য, ১০: ৪।
২৭. মাজহিমা নিকয়া, ৮৯।
২৮. লিঙ, দ্য বুদ্ধা, ১৪০-৫২; মাইকেল এডোয়ার্ডস, ইন দ্য ব্লোইং আউট অভ আ ফ্লেইম: দ্য ওঅর্ল্ড অভ দ্য বুদ্ধা অ্যান্ড দ্য ওঅর্ল্ড অভ ম্যান, লন্ডন, ১৯৭৬, ৩০-৩১।
২৯. গমব্রিচ, থেরাভেদা বুদ্ধজম, ৮১-৮৬; মাইকেল কারিথার্স, দ্য বুদ্ধা, অক্সফোর্ড ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৩, ৯৫-৯৭।
৩০. দিঘা-নিয়া, ৩: ১৯১।
৩১. মাজহিমা নিকয়া, ১৪৩।
৩২. লিঙ, দ্য বুদ্ধা, ১৩৫-৩৭; গমব্রিচ, থেরাভেদা বুদ্ধজম, ৭৫-৭৭।
৩৩. কারিথার্স, দ্য বুদ্ধা, ৮৬-৮৭।
৩৪. গমব্রিচ, থেরাভেদা বুদ্ধজম, ৭৮।
৩৫. আঙুত্তারা নিয়া, ২: ৬৯-৭০।
৩৬. দিঘা নিকয়া, ৩: ১৮০-৮৩।
৩৭. আঙুত্তারা নিকয়া ৪: ৪৩-৪৫।
৩৮. সাম্যত্তা নিকয়া, ৩: ১-৮।
৩৯. শাব্বাত, 31A:cf, ম্যাথু, ৭: ১২; কনফুসিয়াস, অ্যানালেক্টস, ১২: ৪০. আঙুত্তারা নিকয়া ৩: ৬৫।
৪১. প্রাগুক্ত।
৪২. প্রাগুক্ত।
৪৩. সুত্তা নিপাতা, ১১৮।
৪৪. বিনয়া: কুলাভাগ্য ১০: ১।
৪৫. দিঘা নিকয়া, ১৬; ইসালেইন ব্লিউ হর্নার, উইমেন আন্ডার প্রিমিটিভ বুদ্ধজম, লন্ডন, ১৯৩০, ২৮৭।
৪৬. রিটা এম. গ্রস, ‘বুদ্ধজম’ জাঁ হল্মে’র (জন বাউকারের সঙ্গে) সম্পা. উইমেন ইন রিলিজিয়ন, লন্ডন, ১৯৯৪, ৫-৬; অ্যান ব্যানক্রফট, ‘উইমেন ইন বুদ্ধজম,’ উরসুলা কিং (সম্পা.)-এর উইমেন ইন দ্য ওঅর্ল্ডস রিলিজিয়ন্স, পাস্ট অ্যান্ড প্রেজেন্ট, নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৭।
৪৭. দিঘা নিকয়া, ১৬।
৪৮. লেইলা আহমেদ, উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার ইন ইসলাম, নিউ হাভেন ও লন্ডন, ১৯৯২, ১১-২৯।
৪৯. মাজহিমা নিকয়া, ১২৮।
৫০. সম্মপদ, ৫-৬।
৫১. বিনয়া: মহাভাগ্য, ১০: ৫।
৫২. দত্ত, বুড্ডিস্ট মঙ্কস, ৬৬।
৫৩. ধম্মপদ, ১৮৩-৮৫।
৫৪. গমব্রিচ, থেরাভেদা বুদ্ধজম, ৯২; অলদেনবার্গ, দ্য বুদ্ধা: হিজ লাইফ, হিজ ডকট্রিন, হিজ অর্ডার (অনু. উইলিয়াম হোয়ে), লন্ডন, ১৮৮২,xxxiii।
৫৫. গমব্রিচ, থেরাভেদা বুদ্ধজম, ৮৮-৮৯।
৫৬. আঙুত্তারা নিকয়া ৪: ৩৬।
৬. পরিনিব্বানা
বুদ্ধের আলোকপ্রাপ্তির পঁয়তাল্লিশ বছর পর শাক্যের মেদালুম্পা শহরে একদিন বিকেলে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর সাথে দেখা করতে এলেন রাজা পাসেনেদি। বৃদ্ধ হয়ে গেছেন তিনি। সম্প্রতি বুদ্ধের কাছে মন্তব্য করেছেন রাজনৈতিক জীবন ক্রমেই সহিংস হয়ে উঠেছে। রাজাগণ ‘ক্ষমতা মদমত্ত’ ও ‘লোভে আচ্ছন্ন’ হয়ে আছেন; ক্রমাগত ‘হাতি, ঘোড়া, রথ ও পদাতিক বাহিনী’ ব্যবহার করে যুদ্ধে লিপ্ত।[১] গাঙ্গেয় উপত্যকা যেন বিধ্বংসী অহমবাদে পরিচালিত হচ্ছে। বহু বছর ধরে মগধের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে আসছিল কোসালা। এলাকায় একক শাসন কায়েম করার প্রয়াস পাচ্ছিল মগধ। পাসেনেদি স্বয়ং নিঃসঙ্গ হয়ে পরেছিলেন। সম্প্রতি তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীর প্রয়াণ হয়েছে, গভীর বিষণ্নতায় আক্রান্ত ছিলেন তিনি। অন্য মুমূর্ষু মানুষের উপর আস্থা স্থাপন করলে এমনটাই ঘটে। জগতের কোথাওই স্বস্তি বোধ করতে পারছিলেন না পাসেনেদি: ভবঘুরে সন্ন্যাসীদের ‘গৃহত্যাগে’র অনুকরণে প্রাসাদ ছেড়ে সেনাবাহিনী নিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে এক জায়গা হতে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। এমনি এক উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণের সময় শাক্যে আসার পর জানতে পান যে কাছেই বুদ্ধ অবস্থান করছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সঙ্গ লাভের তীব্র আকাঙ্ক্ষা বোধ করেন তিনি। বুদ্ধ, ভাবলেন তিনি, তাঁকে বিশাল মহীরুহের কথা মনে করিয়ে দেয়: শান্ত, বিচ্ছিন্ন, জগতের তুচ্ছ ঝামেলার ঊর্ধ্বে। কিন্তু সংকটে আপনি যেখানে আশ্রয় নিতে পারেন। চট করে মেদালুম্পায় চলে এসেছেন তিনি। পথঘাট দুর্গম হয়ে ওঠায় ঘোড়ার পিঠ হতে নেমে তরবারি আর রাজকীয় পাগড়ি সেনাকর্তা দিঘা কারায়নার হেফাযতে রেখে পায়ে হেঁটে বুদ্ধের কুঁড়ের উদ্দেশে এগিয়েছেন তিনি। বুদ্ধ দরজা খুলে দিলে পাসেনেদি তাঁর পায়ে চুমু খেলেন। ‘এই বৃদ্ধ বেচারাকে কেন এই সম্মান দিচ্ছ?’ জিজ্ঞেস করলেন বুদ্ধ। কারণ আরামা তাঁর জন্যে খুবই স্বস্তিকর, জবাব দিলেন পাসেনেদি: কারণ সংঘ স্বার্থপরতা, সহিংসতা ও রাজ দরবারের লোভ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু সবার ওপরে, উপসংহার টানেন পাসেনেদি, ‘আশীর্বাদপ্রাপ্ত জনের যেমন আশি বছর বয়স, আমারও তাই।’[২] দুজন বৃদ্ধ মিলিত হয়েছেন, বিষণ্ন এই জগতে পরস্পরের প্রতি মমতা প্রকাশ করা উচিৎ তাঁদের।
দিঘা কারায়নাকে যেখানে রেখেছিলেন কুঁড়ে থেকে বিদায় নিয়ে পাসেনেদি সেখানে ফিরে এসে দেখলেন সেনাপ্রধান রাজকীয় প্রতীকসহ চলে গেছেন। সেনাদল যেখানে শিবির ফেলেছে দ্রুত সেখানে এসে দেখলেন কেউ নেই। কেবল একটা ঘোড়া আর তরবারি নিয়ে পরিচারিকাদের একজন রয়ে গেছে। সাবস্তিতে ফিরে গেছেন দিঘা কারায়না, রাজাকে বলল সে। পাসেনেদির উত্তরসুরি রাজকুমার বিদুদভকে সিংহাসনে বসাতে অভ্যুত্থানের আয়োজন করছেন। জীবনের মায়া থাকলে পাসেনেদি যেন সাবস্তি ফিরে না যান। বৃদ্ধ রাজা মগধে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন, কেননা বৈবাহিক সূত্রে রাজকীয় পরিবারের আত্মীয় ছিলেন তিনি। কিন্তু দীর্ঘ যাত্রা ছিল সেটা। চলার পথে পাসেনেদিকে স্বাভাবিকের চেয়ে নিম্নমানের খাবার ও দুর্গন্ধময় পানি খেতে হলো। রাজাগহে পৌঁছে দেখলেন তোরণ বন্ধ হয়ে গেছে। সস্তা সরাইখানায় ঘুমাতে বাধ্য হলেন তিনি। সেরাতে মারাত্মক পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে ভোর হবার আগেই মারা গেলেন। বৃদ্ধের জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা চালানো পরিচারিকা গোটা শহরকে জাগিয়ে তুলল: ‘দুই দেশের শাসক আমার প্রভু কোসালার রাজা ভিখিরির মতো মারা গেছেন। বিদেশের এক শহরের বাইরে মামুলি ভিখেরির সরাইখানায় পড়ে আছেন এখন!’[৩]
বৃদ্ধ বয়সকে বরাবরই দুঃখের প্রতীক হিসাবে দেখেছেন বুদ্ধ যা সকল মরণশীল সত্তাকে আক্রান্ত করে। পাসেনেদি যেমন মন্তব্য করেছিলেন, তিনি স্বয়ং বুড়িয়ে গেছেন। আনন্দ নিজেও যদি এখন আর তরুণ নেই, প্রভুর মাঝে পরিবর্তন লক্ষ করে সম্প্রতি হতাশা বোধ করেছেন তিনি। তাঁর চামড়া কুঁচকে গেছে, হাত-পা থলথলে হয়ে গেছে, দেহ কুঁজো, অনুভূতি যেন দুর্বল হয়ে আসছে। ‘ঠিক বলেছ, আনন্দ’ সায় দিয়েছেন বুদ্ধ।[৪] বৃদ্ধ বয়স আসলেই নিষ্ঠুর। কিন্তু বুদ্ধের শেষ বছরের কাহিনী বয়সের কারণে কৃচ্ছ্রতা সাধনের বিপর্যয়ের চেয়ে বরং বৃদ্ধ মানুষের নাজুকতার উপরই বেশি আলোকপাত করেছে। উচ্চাভিরাষী তরুণেরা প্রবীনদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, ছেলেরা আপন পিতাদের হত্যা করে। বুদ্ধের জীবনের শেষ পর্যায়ে টেক্সট পবিত্রতার অনুভূতি হারিয়ে যাওয়া সন্ত্রাসের জগৎ নিয়ে আলোচনা করেছে। অহমবাদ পরম শাসক হয়ে দাঁড়িয়েছে; ঈর্ষা, ঘৃণা, লোভ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা সহানুভূতি ও প্রেমময়-দয়ায় প্রশমিত হবার নয়। মানুষের আকাঙ্ক্ষার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ানো যে কাউকে নিষ্ঠুরভাবে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সব রকম শোভনতা ও মর্যাদা অদৃশ্য হয়ে গেছে। প্রায় পঞ্চাশ বছর বুদ্ধ যে বিপদের মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছেন সেই বিপদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে ধর্মগ্রন্থগুলো আমাদের সমাজের সহিংসতা ও নিষ্ঠুরতার মুখোমুখি হতে বাধ্য করে যার বিরুদ্ধে আপন স্বার্থহীনতা ও প্রেমময়-দয়ার সংগ্রাম সূচনা করেছিলেন তিনি।
এমনকি সংঘও এই লৌকিক চেতনা মুক্ত ছিল না। আট বছর আগে আরও একবার সংঘাতের কারণে হুমকির মুখে পড়েছিল সংঘ এবং সাঁইত্রিশ বছর ধরে বুদ্ধের নিবেদিতপ্রাণ অনুসারী আরেক বৃদ্ধ রাজা বিম্বিসারাকে হত্যার ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছিল। কেবল বিনয়াতেই আমরা এই বিদ্রোহের পূর্ণ বিবরণ পাই। এটা সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক নাও হতে পারে, তবে সতর্ক বাণী প্রকাশ করে: এমনকি সংঘের নীতিমালা লঙ্ঘিত হতে পারে এবং মারাত্মক করে তোলা যেতে পারে। বিনয়া অনুসারে নাটের গুরু ছিলেন বুদ্ধের শ্যালক দেবদত্ত। কাপিলাবাস্তুতে বুদ্ধের প্রথম বাড়ি সফরের পর সংঘে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। পরবর্তী কালের ধারাভাষ্যসমূহ আমাদের বলে যে দেবদত্ত তরুণ বয়স হতেই বিদ্বেষ পরায়ণ ছিলেন। একসঙ্গে বেড়ে ওঠার সময় থেকেই তরুণ গৌতমের তীব্র প্রতিপক্ষ ছিলেন তিনি। কিন্তু পালি টেক্সট এ সম্পর্কে কিছুই জানে না, দেবদত্তকে ব্যক্রিমহীনভাবে নিবেদিতপ্রাণ সন্ন্যাসী হিসাবে উপস্থাপন করেছে। তিনি মেধাবী বাগ্মী ছিলেন বলে মনে হয়। বুদ্ধ বৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবদত্ত সংঘে তাঁর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন। নিজস্ব শক্তি বলয় গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন তিনি। ধর্মীয় জীবনের সবরকম অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছিলেন দেবদত্ত। নিষ্ঠুরভাবে আত্মপ্রচারণা শুরু করেছিলেন; তাঁর দৃষ্টি সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল: ভালোবাসায় পৃথিবীর চতুর্কোণে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হওয়ার বদলে সম্পূর্ণ নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন, ঘৃণা ও ঈর্ষার হারিয়ে গেছেন। প্রথমে মগধের সেনাপ্রধান ও রাজা বিম্বিসারার উত্তরসুরি রাজকুমার অজাতাশত্তুর শরণাপন্ন হলেন তিনি। ইদ্ধির চোখ ঝলসানো প্রদর্শনীতে মুগ্ধ করে ফেললেন রাজকুমারকে, আপন যোগির ক্ষমতাকে কলুষিত করার সুস্পষ্ট লক্ষণ। কিন্তু দেবদত্তের পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হলেন রাজকুমার: প্রতিদিন রাজাগহের উপকণ্ঠে শকুন-চূড়ার আরামায় দেবদত্তের কাছে ভিক্ষুদের জন্যে বিপুল খাবারভর্তি পাঁচশো রথ পাঠাতে লাগলেন। আনুকূল্যপ্রাপ্ত রাজ-সন্ন্যাসীতে পরিণত হলেন দেবদত্ত। তোষামোদ তাঁর মাথা খারাপ করে দিয়েছিল, তিনি সংঘের নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু শ্যালকের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে বুদ্ধকে যখন সতর্ক করা হলো, অবিচলিত রইলেন তিনি। এইয়াত্রার অদক্ষ আচরণ দেবদত্তের জন্যে কেবল তিক্ত পরিসমাপ্তিই ডেকে আনতে পারে।[৫]
বুদ্ধ যখন রাজাগহের বাইরে বাঁশ বনে অবস্থান করছিলেন, সেই সময় প্রথম প্রচেষ্টা চালান দেবদত্ত। ভিক্ষুদের এক বিরাট সমাবেশে দেবদত্ত আনুষ্ঠানিকভাবে বুদ্ধকে পদত্যাগ করে সংঘের নিয়ন্ত্রণ তাঁর হাতে ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব রাখেন। ‘আশীর্বাদপ্রাপ্ত জন এখন বৃদ্ধ হয়েছেন, বহু বছরের বয়সের ভারে ক্লান্ত…জীবনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছেন,’ তোষামোদের সুরে বললেন তিনি। ‘এখন তাঁকে বিশ্রাম নিতে দাও।’ প্রবলভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন বুদ্ধ: এমনকি তাঁর দুই প্রধান অনুসারী সারিপুত্ত ও মগ্গালানার হাতেও সংঘ তুলে দেবেন না তিনি। দেবদত্তের মতো এমন বেপথু মানুষকে কেন এমন পদ দিতে যাবেন? অপমানিত ও হিংস্র হয়ে উঠলেন দেবদত্ত, প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে আরামা ত্যাগ করলেন। সংগঠনের নেতৃত্ব নিয়ে তেমন একটা উদ্বিগ্ন ছিলেন না বুদ্ধ। তিনি বরাবরই জোর দিয়ে এসেছেন, সংঘের, কোনও কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বপূর্ণ ব্যক্তির প্রয়োজন নেই, কেননা প্রত্যেক সন্ন্যাসী তার নিজের জন্যে দায়ী। কিন্তু বিরোধ সৃষ্টি করার যেকোনও প্রয়াস, দেবদত্ত যেমন করেছেন, অশুভ। অহমবাদ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বৈরিতা ও প্রতিযোগিতার পরিবেশ আধ্যাত্মিক জীবনের সঙ্গে মোটেই মানানসই নয়, সংঘের মূল উদ্দেশ্যকেই তা নাকচ করে দেবে। তো বুদ্ধ প্রকাশ্যে নিজেকে এবং সংঘকে দেবদত্ত হতে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে সারিপুত্তকে রাজাগহে দেবদত্তকে নিষিদ্ধ করার নির্দেশ দিলেন। ‘আগে,’ ব্যাখ্যা দিলেন তিনি, ‘এক রকম স্বভাব ছিল দেবদত্তের, এখন ভিন্ন স্বভাব হয়েছে তার।’ কিন্তু ক্ষতি যা হবার হয়ে গিয়েছিল। শহরবাসীদের কেউ কেউ বিশ্বাস করেছিল যে রাজকুমারের সঙ্গে দেবদত্তের নতুন সখ্যতায় ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছেন বুদ্ধ। কিন্তু অধিকতর বিবেচনা সম্পন্ন ব্যক্তিরা কোনও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেনি।[৬]
এদিকে রাজপুত্র অজাতাশত্তুর কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে হাজির হলেন দেবদত্ত। আগের দিনে, বললেন তিনি, মানুষের আয়ু এখনকার চেয়ে বেশি ছিল। রাজা বিম্বিসারা এখনও টিকে আছেন। অজাতাশত্তু হয়তো কোনওদিনই সিংহাসনে বসতে পারবেন না। বাবাকে তিনি হত্যা করছেন না কন? দেবদত্ত অন্যদিকে বুদ্ধকে হত্যা করতে পারেন। এই দুই বৃদ্ধ কেন তাঁদের পথে বাধা হয়ে থাকবেন? দেবদত্ত ও অজাতাশত্তু চমৎকার একটা জুটি হতে পারতেন। অসাধারণ সাফল্য অর্জন করা যাবে। বুদ্ধিটা রাজপুত্রের মনে ধরল। কিন্তু ঊরুতে ছুরি বেঁধে রাজার অন্দরমহলে লুকিয়ে ঢোকার সময় আটক করা হয় তাঁকে। তিনি সমস্ত অপরাধ স্বীকার করেন। গুপ্তহত্যার পরিকল্পনায় দেবদত্তের ভূমিকা জানার পর সেনাবাহিনীর কিছু কর্মকর্তা গোটা সংঘকে শেষ করে দিতে চেয়েছিলেন,, কিন্তু বিম্বিসারা যুক্তি দেখান যে বুদ্ধ আগেই দেবদত্তকে বহিষ্কার করেছেন, এই দুষ্কৃতকারীর কর্মকাণ্ডের জন্যে তাঁকে দায়ী করা যাবে না। অজাতাশত্তুকে তাঁর সামনে হাজির করার পর রাজা বিষণ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন কেন তিনি তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছেন। আমি রাজত্ব চাই, মহামান্য।’ খোলাখুলি জবাব দিলেন অজাতাশত্তু। অযথা এতদিন বুদ্ধের অনুসারী ছিলেন না বিম্বিসারা। ‘যদি রাজত্ব চেয়ে থাক, রাজকুমার,’ সহজ কণ্ঠে বললেন তিনি। ‘এরাজ্য তোমার।’[৭] পাসেনেদির মতো তিনিও সম্ভবত রাজনীতির জন্যে প্রয়োজনীয় অদক্ষ ও আগ্রাসী আবেগ সম্পর্কে সজাগ ছিলেন, তাই জীবনের শেষ কটি বছর আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করে কাটিয়ে দিতে চেয়েছেন। অবশ্য সিংহাসন ত্যাগ কোনও উপকার হয়নি তাঁর। সেনাবাহিনীর সমর্থনে অজাতাশত্তু বাবাকে গ্রেপ্তার করান এবং উপোস মৃত্যুবরণ করেন তিনি।
নতুন রাজা এরপর বুদ্ধকে হত্যার দেবদত্তের পরিকল্পনায় মদদ যোগান। সেনাবাহিনী হতে প্রশিক্ষিত গুপ্তঘাতক সরবরাহ করেন তিনি। কিন্তু ওদের একজন তীর-ধনুক নিয়ে তাঁর কাছাকাছি যাবার পরেই আতঙ্কে স্থির হয়ে যায়। ‘এসো, বন্ধু,’ কোমল কণ্ঠে বলেন বুদ্ধ। ‘ভয় পেয়ো না।’ নিজের কাজের ভুল বুঝতে পারায় তার অন্যায় ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। বুদ্ধ এরপর সৈন্যটিকে সাধারণ মানুষের উপযোগি নির্দেশনা দিলেন। খুবই অল্প সময়ের ভেতর অনুতপ্ত ঘাতক একজন শিষ্যে পরিণত হয়েছিল। একের পর এক তার সতীর্থ ষড়যন্ত্রীরা অনুসরণ করল।[৮] এরপর ব্যাপারটা নিজের হাতে তুলে নিতে বাধ্য হলেন দেবদত্ত। প্রথমে বুদ্ধকে চাপা দেওয়ার জন্যে পাহাড় চূড়া হতে এক বিরাট পাথর গড়িয়ে দিলেন তিনি, কিন্তু বুদ্ধের পায়ে সামান্য আঘাত লাগা ছাড়া অন্য কোনও ক্ষতি হলো না। এরপর নীলগিরি নামে এক হিংস্র হাতি ছেড়ে দিলেন বৃদ্ধের পেছনে। কিন্তু শিকারকে দেখামাত্র বুদ্ধ হতে উৎসারিত প্রেমের তরঙ্গে পরাস্ত হয়ে শুঁড় নামিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে পড়ল নীলগিরি। ওটার কপালে হাত বুলিয়ে দিলেন বুদ্ধ। ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন, সহিংসতা আগামী জন্মে কোনও উপকারে আসবে না তার। নীলগিরি বুদ্ধের পায়ের কাছ থেকে শুঁড় দিয়ে বালি টেনে নিজের মাথায় ছিটাল, পিছিয়ে গেল তারপর। বুদ্ধ দৃষ্টির আড়ালে না যাওয়া পর্যন্ত তৃষ্ণার্ত চোখে তাকিয়ে রইল তাঁর দিকে। এরপর শান্ত পায়ে আস্ত বিলের দিকে ফিরে গেল। সেদিন থেকে বদলে যাওয়া এক পশু।[৯]
বুদ্ধ যেন এইসব আক্রমণ হতে সুরক্ষিত, এটা বুঝতে পেরে ষড়যন্ত্রকারীরা কৌশল বদল করল। ক্ষমতা দখলের প্রয়াসে সফল অজাতাশতু দেবদত্তকে ঝেড়ে ফেলে বুদ্ধের একজন সাধারণ শিষ্যে পরিণত হলেন। এবার নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন দেবদত্ত, সংঘের অভ্যন্তরে সমর্থন যোগাড়ের প্রয়াস পেলেন তিনি। বেসালির কিছু তরুণ, অনভিজ্ঞ সন্ন্যাসীর কাছে বুদ্ধের মধ্যপন্থা ঐতিহ্য হতে অগ্রহণযোগ্য বিচ্যুতি বলে প্রচার করলেন। বৌদ্ধদের উচিৎ অধিকতর ঐতিহ্যবাহী সাধকদের কঠোর আদর্শে ফিরে যাওয়া। পাঁচটি নতুন বিধানের প্রস্তাব রাখলেন দেবদত্ত: বর্ষাকালে আরামার বদলে সংঘের সকল সদস্যকে বনে-জঙ্গলে বাস করতে হবে; তাদের অবশ্যই কেবল ভিক্ষার উপর নির্ভর করতে হবে, সাধারণের বাড়িতে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারবে না; নতুন জোব্বার বদলে অবশ্যই রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া ন্যাকড়া পরতে হবে; কুঁড়ে ঘরের বদলে অবশ্যই খোলা জায়গায় ঘুমাতে হবে; এবং তারা কখনও জীবিত প্রাণীর মাংস খেতে পারবে না।[১০] এই পাঁচটি বিধান দেবদত্তের পক্ষত্যাগের ঐতিহাসিক মূল সত্য তুলে ধরতে পারে। রক্ষণশীল ভিক্ষুদের কেউ কেউ হয়তো সংগঠনের ক্রমাবনতিতে উদ্বিগ্ন হওয়ায় মূল সংঘ হতে বেরিয়ে যাবার প্রয়াস পেয়েছিলেন। দেবদত্ত এই সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত থেকে থাকতে পারেন। তাঁর প্রতিপক্ষ বুদ্ধের মধ্যপন্থার পক্ষাবলম্বীরা হয়তো বিনয়ায় প্রাপ্ত নাটকীয় কিংবদন্তী আবিষ্কার করে দেবদত্তের নামে কালিমা লেপন করতে চেয়েছেন।
দেবদত্ত তাঁর পঞ্চবিধান প্রকাশ করে বুদ্ধকে সমগ্র সংঘের জন্যে তা বাধ্যতামূলক করার আহ্বান জানালে যেকোনও সন্ন্যাসীই তাঁর খুশিমতো জীবন যাপনের অধিকারী বলে প্রত্যাখ্যান করলেন বুদ্ধ, এইসব ব্যাপারে জবরদস্তি সংগঠনের চেতনার পরিপন্থী। সন্ন্যাসীদেরই মনস্থির করতে হবে, তাদের কারও নির্দেশনা অনুসরণে বাধ্য করা যাবে না। উল্লসিত হয়ে উঠেছিলেন দেবদত্ত। বুদ্ধ তাঁর ন্যায় অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন! অনুসারীদের কাছে বিজয়ীর সুরে তিনি ঘোষণা দিলেন, বুদ্ধ বিলাসিতার কাছে নতি স্বীকার করে আত্মতুষ্টিতে নিপতিত হয়েছেন। এখন দুর্নীতিগ্রস্ত ভাই হতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া তাদের দায়িত্ব।[১১] পাঁচশো অনুসারী নিয়ে রাজাগহের উপকণ্ঠে গয়াশিসা পাহাড়ে শিবির গাড়লেন দেবদত্ত, অন্যদিকে বিদ্রোহী ভিক্ষুদের ফিরিয়ে আনতে সারিপুত্ত ও মগ্গালানাকে পাঠালেন বুদ্ধ। তাঁদের আসতে দেখে দেবদত্ত ধরে নিলেন বুদ্ধকে ত্যাগ করে তাঁর দলে যোগ দিতে আসছেন ওরা। উল্লসিত হয়ে শিষ্যদের একটা সভা ডাকলেন তিনি, গভীর রাত পর্যন্ত বক্তব্য রাখলেন। তারপর পিঠ ব্যথার কথা বলে সারিপুত্ত ও মগ্গালানাকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দিয়ে শুতে চলে গেলেন। এই দুজন বিশ্বস্ত নেতা বক্তব্য শুরু করার পর অচিরেই ভিক্ষুদের বুদ্ধের কাছে ফিরে যেতে রাজি করিয়ে ফেললেন। কোনওরকম শাস্তি ছাড়াই তাঁদের বরণ করে নেন বুদ্ধ।[১২] কোনও কোনও টেক্সট আমাদের বলে, দেবদত্ত আত্মহত্যা করেছেন। অন্যগুলোর মতে বুদ্ধের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছার আগেই মারা যান তিনি। এইসব কাহিনীর সত্য যাই হোক, বৃদ্ধ বয়সের ভোগান্তি সম্পর্কে সত্যি কথা জানায়। সতর্কতামূলক কাহিনীও শোনায়। এমনকি সাধারণ জনজীবনে প্রকট স্বার্থপরতা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর মতানৈক্য হতে সংঘও মুক্ত ছিল না।
জীবনের শেষ বছরে এই বিপদ নিয়ে আলোচনা করেছেন বুদ্ধ। এখন আশি বছর বয়স্ক তিনি। রাজা অজাতাশত্তু ততদিনে মগধের সিংহাসনে দারুণভাবে অধিষ্ঠিত। প্রায়ই বুদ্ধের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। মাল্লা, বিদেহা, লিচাবি, কোলিয়া ও বাজ্জির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানানোর পরিকল্পনা করছিলেন তিনি। তাঁর রাজ্যের পুবে অবস্থিত এই রাজ্যগুলো ‘বাজ্জিয়’ নামে একটা প্রতিরক্ষা সংগঠন গড়ে তুলেছিল। তাদের মানচিত্র থেকে মুছে ফেলে নিজের রাজ্যের অঙ্গীভূত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন রাজা। কিন্তু আক্রমণ শুরু করার আগে বাসাকারা নামে একজন ব্রাহ্মণ মন্ত্রীকে তিনি কী করতে যাচ্ছেন বুদ্ধকে জানাতে ও মনোযোগ দিয়ে বুদ্ধের মন্তব্য শুনবার নির্দেশ দিয়ে পাঠালেন তাঁর কাছে। বুদ্ধ ছিলেন দুর্বোধ্য, বাসাকারাকে তিনি বললেন বাজ্জীয়রা যতক্ষণ প্রজাতন্ত্রীয় ঐতিহ্য মেনে চলছে, ‘ঘনঘন উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি নিয়ে সভা করছে,’ মতৈক্যের মাঝে জীবন কাটাচ্ছে, প্রবীনদের সমান দেখাচ্ছে, মনোযোগ দিয়ে তাদের পরামর্শ শুনছে, এবং পূর্বসুরিদের আইন ও ধার্মিকতা পালন করছে, ততক্ষণ রাজা অজাতাশত্তু তাদের পরাস্ত করতে পারবেন না। মনোযোগ দিয়ে শুনলেন বাসাকারা, তারপর বুদ্ধকে বললেন বাজ্জীয়রা যেহেতু এখন এই সমস্ত শর্তই মেনে চলছে সেহেতু এখন তারা অপরাজেয়। তিনি রাজাকে এই সংবাদ দিতে ফিরে গেলেন।[১৩] অবশ্য বৌদ্ধিয় কিংবদন্তীতে আছে এর অল্প কিছুদিন পরেই রাজা অজাতাশত্তু বাজ্জকীয়দের পরাস্ত করতে সক্ষম হন। নেতাদের মাঝে অনৈক্যের বীজ বপন করার জন্যে এইসব প্রজাতন্ত্রে গুপ্তচর পাঠিয়ে এই সাফল্য অর্জন করেন তিনি। বাসাকারা বিদায় নেওয়ার পর দরজার আড়ালে বুদ্ধের উচ্চারিত কথায় তাই এক ধরনের তাগিদ ও মর্মস্পর্শী সুর ছিল। সংঘের ক্ষেত্রেও একই শর্ত আরোপ করেন তিনিঃ যতক্ষণ এর সদস্যরা প্রবীন ভিক্ষুদের সম্মান করবে, ঘনঘন সম্মেলন অনুষ্ঠান করবে ও ধম্মের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত থাকবে ততদিন সংঘ টিক থাকবে।
গোত্রীয় প্রজাতন্ত্রগুলো অনিবার্য ধ্বংসের মুখে ছিল। সেগুলো ছিল অতীতের অংশ এবং অচিরেই নতুন উগ্র শাসকদের করতলগত হবে। রাজা পাসেনেদির ছেলে বুদ্ধের নিজ গোত্র শাক্যদের অচিরেই পরাস্ত করে হতালীলা চালাবেন। কিন্তু বুদ্ধের সংঘ ছিল নতুন, হালনাগাদ এবং পুরোনো প্রজাতান্ত্রিক সরকারগুলোর দক্ষ আধ্যাত্মিক রূপ। অধিকতর সহিংস ও নিপীড়ক শাসকগণ যেসব মূল্যবোধ হারানোর হুমকির মুখে ছিল সেগুলোই কঠোরভাবে অনুসরণ করে যাবে সংঘ। কিন্তু এ জগৎ বিপদসংকুল। সংঘ আভ্যন্তরীণ মতানৈক্য, প্রবীনদের অসম্মান, প্রেমময়-দয়ার ঘাটতি ও দেবদত্তের কেলেঙ্কারীর সময় আবির্ভূত অগভীরতা হতে বাঁচতে পারবে না। ভিক্ষু ও ভিক্ষুনিদের অবশ্যই মনোযোগি হতে হবে, আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে সতর্ক আর ধ্যানমূলক অনুশীলনের প্রতি উদ্যমী ও বিশ্বস্ত থাকেত হবে যা আলোক বয়ে আনতে পারে। সন্ন্যাসীরা যতদিন ‘গল্পগুজব, অলস সময় কাটানো আর মেলামেশা’র মতো অদক্ষ কাজ এড়িয়ে যাবেন, ‘যত দিন তাদের নীতিবর্জিত বন্ধু থাকবে না এবং এধরনের মানুষের প্রভাবে পড়া এড়াতে পারবেন, যতদিন তাঁরা সন্ধানের মাঝপথে বিরতি দিয়ে মাঝারি পর্যায়ের আধ্যাত্মিকতায় সন্তুষ্ট হবেন না’[১৪] ততদিন সংগঠনের অবনতি ঘটবে না। তাঁরা এতে ব্যর্থ হলে আর পাঁচটা ধর্ম নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ভিন্ন কিছু থাকবে নাঃ শাসকদের দুর্নীতির শিকারে পরিণত হবে এটা, চরমভাবে দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়বে।
বাসাকারার সঙ্গে সভার পর রাজাগহ ছেড়ে বেসালিতে বাস্যা অবকাশ যাপন করবেন বলে উত্তরে রওনা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন বুদ্ধ। যেন রাজা অজাতাশত্তুর ‘বাজ্জীয়দের নিশ্চিহ্ন করার’ পরিকল্পনার প্রকাশ মুহূর্তের জন্যে বিতৃষ্ণ করে তুলেছিল তাঁকে, অবরুদ্ধ প্রজাতন্ত্রগুলোর প্রতি তাঁর দরদ সম্পর্কে সজাগ করে তুলেছিল। কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় কোসালা ও মগধে কাটিয়েছেন তিনি, সেখানে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সম্পন্ন করেছেন। কিন্তু এখন এই রাজ্যগুলোর রাজনৈতিক জীবনকে চালিতকারী আগ্রাসনের শিকার একজন বৃদ্ধ গাঙ্গেয় উপত্যকার আরও প্রত্যন্ত এলাকার উদ্দেশে চলেছেন।
ধীর গতিতে সন্ন্যাসীদের বিরাট একটা দল নিয়ে মগধ এলাকা হয়ে প্ৰথমে নালন্দা ও তারপর মহান বৌদ্ধ রাজা অশোকের রাজধানী (২৬৯-২৩২ বিসিই) পাটালিগামে (আধুনিক পাটলা) পৌঁছেন তিনি। অশোক এমন এক রাজ্য গড়ে তুলবেন যা সহিংসতাকে এড়িয়ে ধম্মের সহানুভূতির নীতিমালা গ্রহণের প্রয়াস পেয়েছিল। বুদ্ধ বাজ্জীয়দের বিরুদ্ধে আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে মগধের মন্ত্রীদের নির্মাণাধীন সুবিশাল দুর্গ লক্ষ করলেন, শহরের ভবিষ্যৎ খ্যাতির ভবিষ্যদ্বাণী করলেন তিনি। সাধারণ ভক্তরা এখানে গালিচা বিছিয়ে, বড় বড় কুপি জ্বালিয়ে বুদ্ধকে একটা বিশ্রাম ঘর ছেড়ে দিল। সারারাত সাধারণ মানুষের প্রয়োজন উপযোগি করে তোলা ধম্ম ব্যাখ্যা করলেন বুদ্ধ। তিনি উল্লেখ করলেন, দক্ষ আচরণ এই জগতেও একজন শুদ্ধ নারী বা শুদ্ধ পুরুষের জন্যে উপকারী হতে পারে। তাদের তাীবনেও আলোকনের পথে অগ্রসর হওয়া নিশ্চিত করবে।[১৫]
অবশেষে বেসালি পৌঁছলেন বুদ্ধ। প্রথমে সমস্ত কিছু যেমন ছিল বরাবর তেমনই মনে হলো। অন্যতম নেতৃস্থানীয় পতিতা আম্বাপালির আম- বাগানে উঠলেন তিনি। বুদ্ধকে স্বাগত জানাতে রথের বহর নিয়ে হাজির হলো সে। ধম্ম শুনবার জন্যে তাঁর পায়ের কাছে বসল। বুদ্ধকে খাবারের আমন্ত্রণ জানাল। তিনি যখন সম্মতি দিয়েছেন, বেসালিতে বসবাসকারী লিছাবি গোত্রের সদস্যরা চমৎকারভাবে রঙ করা রথের মিছিল নিয়ে দলবেঁধে বুদ্ধকে আমন্ত্রণ জানাতে অগ্রসর হলো। অপূর্ব দৃশ্য ছিল সেটা। দেখে মুচকি হাসলেন বুদ্ধ, ভিক্ষুদের বললেন, স্বর্গের দেবতাদের চমৎকারিত্বের খানিকটা ধারণা আছে ওদের। বুদ্ধের চারপাশে ঘিরে বসল লিছাবিবাসীরা, বুদ্ধ তাদের ধম্মর বাণী দিয়ে ‘উদ্দীপ্ত, অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত’ করলেন। এই আলোচনার শেষে লিছাবিরা তাদের আমন্ত্রণের কথা জানাল। বুদ্ধ যখন বললেন তিনি আগেই আম্বাপালির নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছেন, মনঃক্ষুণ্ণ হলো না তারা, তুড়ি বাজিয়ে চিৎকার করে উঠল, “ওহ, আম্বপালি আমাদের হারিয়ে দিয়েছে, বুদ্ধিতে হারিয়ে দিয়েছে।’ সেরাতে খাবারের সময় বারবণিতা তার আম-বাগানটি সংঘকে দান করে দেয়। বুদ্ধ কিছুদিন সেখানে অবস্থান করে ভিক্ষুদের দীক্ষা দেন। বুদ্ধকে ঘিরে স্বাভাবিক ব্যস্ততা, জাঁক ও উত্তেজনা ছিল, এবং তার মূলে অভিনিবেশ ও ধ্যানের নিবিড় অন্তস্থ জীবনের জন্যে এক অব্যাহত প্রেরণা।[১৬]
কিন্তু তারপর দৃশ্যপট মলিন হয়ে উঠতে শুরু করল। সন্ন্যাসীদের নিয়ে বেসালি ত্যাগ করে নিকটস্থ বেলুভাগামাকা গ্রামে অবস্থান গ্রহণ করেন বুদ্ধ। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করার পর আকস্মিকভাবে সন্ন্যাসীদের বিদায় করে দিলেন তিনি। তাদের বেসালিতে ফিরে যেতে হবে। যেখানে সম্ভব বর্ষার অবকাশের জন্যে অবস্থান নিতে হবে। তিনি আর আনন্দ বেলুভাগামাকায় রয়ে যাবেন। বুদ্ধের জীবনে এক নতুন নিঃসঙ্গতার পর্যায় প্রবেশ করেছে। এই পর্যায় থেকে তিনি যেন বড় বড় শহর-নগর এড়িয়ে আরও অচেনা অজানা জায়গার খোঁজ করছিলেন। যেন এরই মধ্যে জগৎ ত্যাগ করতে শুরু করেছিলেন। ভিক্ষুরা বিদায় নেওয়ার পর মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন বুদ্ধ। কিন্তু প্রবল আত্মনিয়ন্ত্রণের সাহায্যে যন্ত্রণা আড়াল করে অসুস্থতা কাটিয়ে ওঠেন। তাঁর পক্ষে এখুনি মৃত্যুবরণ করে পরম নিব্বানা (পরিনিব্বানা লাভ করা ঠিক হবে না, বোধি বুক্ষের নিচে অর্জন করা অলোকন যা পূর্ণাঙ্গ করে তুলবে। সবার আগে সংঘকে বিদায় জানাতে হবে। সুতরাং, সেরে উঠলেন বুদ্ধ, অসুস্থতার কামরা হতে বেরিয়ে যে কুঁড়েতে অবস্থান করছিলেন সেটার বারান্দায় আনন্দের সঙ্গে বসলেন।
বুদ্ধের অসুস্থতা আনন্দের অন্তরাত্মা টলিয়ে দিয়েছিল। ‘আশীর্বাদপ্রাপ্তকে আমি স্বাস্থ্যবান, তরতাজা দেখে অভ্যস্থ,’ বুদ্ধের পাশে বসার সময় কাঁপা কণ্ঠে বললেন তিনি। প্রথমবারের মতো উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁর শুরু মারা যেতে পারেন। ‘আমার শরীরের আড়ষ্ট হয়ে যাওয়া টের পেয়েছি,’ বললেন তিনি। ‘আমি ঠিকমতো দেখতে পাই না। আমার মন বিভ্রান্ত।’ কিন্তু একটা কথা ভেবে সান্ত্বনা পেলেন তিনিঃ সংঘের উত্তরাধিকার ও পরিচালনা সম্পর্কে কোনও একটা সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত বুদ্ধ মারা যাবেন না। গুরু বিদায় নেওয়ার পর যা পরিবর্তন হতে বাধ্য। দীর্ঘশ্বাস ফেললেন বুদ্ধ। ‘সংঘ আমার কাছে কী আশা করে, আনন্দ?’ অধৈর্য কণ্ঠে জানতে চাইলেন তিনি। যা শেখানোর ছিল ভিক্ষুরা তার সবই জানেন। কয়েকজন মনোনীত নেতার জন্যে কোনও গোপন মতবাদ নেই। ‘আমাকেই সংঘের পরিচালনা করতে হবে,’ বা ‘আমার ওপর সংঘ নির্ভরশীল,’ এজাতীয় ভাবনা কোনও আলোকপ্রাপ্ত মানুষের মনে আসে না। ‘আমি একজন বৃদ্ধ মানুষ, আনন্দ। আশি বছর বয়স।’ নির্দয় কণ্ঠে বললেন বুদ্ধ। ‘আমার দেহ পুরোনো ঠেলাগাড়ির মতো ঠক্কর ঠক্কর করে চলে। একমাত্র যে কাজটি স্বাচ্ছন্দ ও সতেজতা বয়ে আনে সেটা হচ্ছে ধ্যান, যা তাঁকে নিব্বানার মুক্তির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। সুতরাং প্রত্যেক ভিক্ষু ও ভিক্ষুনির বেলায়ও তাই হওয়া উচিৎ। ‘তোমাদের প্রত্যেককে নিজেকে নিজের দ্বীপে পরিণত করতে হবে। অন্য কাউকে নয়, নিজেকেই নিজের আশ্রয় পরিণত করতে হবে।’ কোনও বৌদ্ধ অন্য কারও ওপর নির্ভর করতে পারে না। সংগঠনে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্যে কারও প্রয়োজন নেই। ‘ধম্ম, কেবল ধৰ্ম্মই তার আশ্রয়।[১৭] ভিক্ষুরা কেমন করে আত্মনির্ভর হবে? উত্তর আগেই জানা আছে তাদের: ধ্যান, মনোসংযোগ, অভিনিবেশ ও জগৎ হতে শৃঙ্খলাপূর্ণ বিচ্ছিন্নতার মধ্য দিয়ে। সংঘের কাউকে পরিচালনা করার প্রয়োজন নেই, কোনও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ নয়। বৌদ্ধদের জীবনধারার মোদ্দা কথা, এমন এক অন্তস্থ উৎস অর্জন করতে হবে যা এই ধরনের নির্ভরশীলতা সম্পূর্ণ হাস্যকর করে তোলে।
কিন্তু আনন্দ এখনও নিব্বানা লাভ করেননি। দক্ষ যোগি ছিলেন না তিনি। আত্ম-নির্ভরশীলতার এই মাত্রা অর্জন করতে পারেননি। ব্যক্তিগতভাবে মনিবের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন তিনি। এই ধরনের যোগ বীরত্বের জন্যে প্রস্তুত নয়, কিন্তু বুদ্ধের প্রতি আরও শ্রদ্ধা (ভক্তি) প্রয়োজন, এমন বৌদ্ধদের আদর্শে পরিণত হবেন, তিনি তাদের উৎসাহিত করার জন্যে। কয়েক দিন পর আরেকটা ধাক্কা খেলেন আনন্দ। জনৈক নবীশ নালন্দা থেকে সারিপুত্ত ও মগ্গালানার মৃত্যু সংবাদ নিয়ে এলো। আবারও আনন্দের দিশাহারা অবস্থা দেখে কিঞ্চিৎ উত্তেজিত বোধ করলেন বুদ্ধ। কী প্রত্যাশা করেছিলেন তিনি? এটাই ধম্মের মূল কথা নয় যে কোনও কিছুই চিরকাল টিকে থাকে না এবং আমরা যা এবং যাকে ভালোবাসি তা থেকে সবসময়ই বিচ্ছেদ ঘটে? আনন্দ কি ভেবেছেন যে, বৌদ্ধরা যে বিধি অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে বেঁচে আছে সারিপুত্ত তা সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন বা সৎগুণের বিধান ও ধ্যানের জ্ঞানও সংঘ হতে বিদায় নিয়েছে? ‘না, প্রভু,’ প্রতিবাদ করলেন হতভাগ্য আনন্দ। আসলে সারিপুত্ত যে কত উদার ছিলেন, ধম্মের ক্লান্তিহীন ব্যাখ্যা দিয়ে কীভাবে সবাইকে সমৃদ্ধ ও সাহায্য করেছিলেন সেটা মনে না করে পারছেন না। দুঃসংবাদ বয়ে আনা নবীশের নিয়ে আসা ভিক্ষার পাত্র ও জোব্বা দেখাটা ছিল এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য। ‘আনন্দ,’ আবার বললেন বুদ্ধ। ‘তোমাদের প্রত্যেককে যার যার দ্বীপ সৃষ্টি করতে হবে, নিজেকে, অন্য কাউকে নয়, নিজের আশ্রয় নির্মাণ করতে হবে: তোমাদের প্রত্যেককে ধম্মকেই তার দ্বীপে পরিণত করতে হবে, ধম্মই, অন্য কিছু নয়, তার আশ্রয়।[১৮]
দুই ঘনিষ্ঠ অনুসারীর মৃত্যুতে দুঃখ পাওয়ার বদলে তাঁরা পরিনিব্বানা লাভ করায় আমোদিত হয়ে উঠেছিলেন বুদ্ধ: মরণশীলতার দুর্বলতাসমূহ হতে পরম মুক্তি। গোটা সংঘের ভালোবাসার পাত্র এমন দুজন অনুসারী থাকাটা তাঁর জন্যে আনন্দের ব্যাপার ছিল। কীভাবে বিমর্ষ হবেন তিনি, বিলাপ করবেন, যেখানে তাঁরা তাঁদের অন্বেষার চরম লক্ষ্যে পৌঁছেছেন?[১৯] তা সত্ত্বেও অনলোকিতজনের জন্যে বুদ্ধের এক ধরনের মর্মপীড়া ও বিষণ্নতা ছিল। আনন্দ ছাড়া একান্তদের আর কেউ ছিল না। টেক্সটসমূহ একে আড়াল করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু উত্তেজিত জনতা ও বন্ধুদের সঙ্গে বর্ণাঢ্য ভোজ আর হয়নি। তার বদলে দুই বৃদ্ধ বুদ্ধ ও আনন্দ একাকী সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। বেঁচে থাকার ক্লান্তি ও সঙ্গীদের বিদায় প্রত্যক্ষ করেছেন যা বুড়ো বয়সের ট্র্যাজিডি নির্মাণ করে। এমনকি বুদ্ধও হয়তো এর খানিকটা স্বাদ পেয়েছিলেন; জোরালোভাবে বিচ্ছিন্ন বোধ করেছেন, ছায়া-সত্তা মারার শেষবারের মতো অবির্ভূত হওয়া তাই বোঝায়। আনন্দ এবং তিনি বেসালির অসংখ্য মন্দিরের একটায় মাত্র সারাদিন একসঙ্গে কাটিয়েছেন। বুদ্ধ মন্তব্য করলেন, চাইলে তাঁর মতো সম্পূর্ণ আলোকপ্রাপ্ত একজন মানুষের পক্ষে ইতিহাসের অবশিষ্ট অংশ পাড়ি দেওয়া সম্ভব। টেক্সট আমাদের বলছে, তিনি আনন্দকে আভাস দিচ্ছিলেন, তিনি যদি তাঁর নির্দেশনাকাঙ্ক্ষী দেবতা ও মানুষের প্রতি সমবেদনার কারণে মর্ত্যে অবস্থান করার আবেদন জানান, বুদ্ধের বেঁচে থাকার ক্ষমতা আছে। কিন্তু তারপরেও, বেচারা আনন্দ মাথা খাটাতে পারেননি। তিনি বুঝতে না পারায় বুদ্ধকে ঐতিহাসিক পর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত সংঘের সঙ্গে অবস্থান করার অনুরোধ জানাননি। এটা এমন এক ভুল ছিল যার জন্যে আদি সংঘের সদস্যগণ আনন্দকে দোষারোপ করেছেন-মনিবের প্রতি বহু বছরের নিবেদিতপ্রাণ সেবার বিনিময়ে অকিঞ্চিৎকর পুরস্কার। স্বয়ং বুদ্ধ যার প্রশংসা করতেন। কিন্তু বুদ্ধ আভাস দেওয়ার পর তার তাৎপর্য বুঝতে পারেননি আনন্দ। কোমল কণ্ঠে মামুলি মন্তব্য করে কাছের একটা খাটের পায়ের কাছে বসতে এগিয়ে যান তিনি।
হয়তো ক্ষণিকের জন্যে হলেও এমনকি বুদ্ধও হয়তো নিজের আয়ু ফুরিয়ে আসছে টের পেয়ে এমন একজন সঙ্গী কামনা করেছিলেন যিনি তাঁর মনের কথা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর ছায়া- সত্তা মারা উপস্থিত হলেন। ‘তথাগতকে এবার পরিনিব্বানা লাভ করতে দাও,’ প্রলুব্ধ করার সুরে ফিসফিস করে বললেন মারা। কেন চালিয়ে যাওয়া? চূড়ান্ত বিশ্রাম পাওনা হয়েছে তাঁর: সংগ্রাম অব্যাহত রাখার কোনও যুক্তি নেই। শেষবারের মতো মারাকে প্রত্যাখ্যান করলেন বুদ্ধ। দায়িত্ব সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত পরিনিব্বানায় প্রবেশ করবেন না তিনি; যতক্ষণ না নিশ্চিত হচ্ছেন যে সংগঠন ও পবিত্র জীবন ঠিকমতো প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কিন্তু, যোগ করলেন তিনি, অচিরেই ঘটবে সেটা: ‘তিন মাসের মধ্য,’ মারাকে বললেন তিনি, ‘তথাগত পরিনিব্বানা লাভ করবে।’[২১]
তারপরই ধর্মগ্রন্থসমূহ আমাদের বলছে যে, বেসালির কাঁপালা মন্দিরে বুদ্ধ সচেতন ও ইচ্ছাকৃতভাবে বেঁচে থাকার ইচ্ছা ত্যাগ করেন। এমন এক সিদ্ধান্ত যা গোটা সৃষ্টিজগতে অনুরণিত হয়েছে। ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল পৃথিবী, আনন্দকেও বুঝিয়ে দিয়েছিল যে অশুভ কিছু আসন্ন। গুরুগম্ভীর ডঙ্কা বাজতে শুরু করেছিল স্বর্গে। বেঁচে থাকার আবেদন জানানোর আর সময় নেই, অনুতপ্ত পরিচারক আনন্দকে বললেন বুদ্ধ। এখন তাঁকে অবশ্যই সংঘের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে হবে। সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক বিদায় নিতে হবে। বেসালির আরামায় বিশাল রঙিন মিলনায়তনে আশপাশে বাসরত সকল ভিক্ষুর উদ্দেশে বক্তব্য রাখলেন তিনি। তাদের নতুন কিছু বলার ছিল না তাঁর। ‘তোমাদের আমি কেবল সেই সব জিনিসই শিক্ষা দিয়েছি যা আমার নিজের পূর্ণ অভিজ্ঞতা রয়েছে,’ বলেন তিনি। বিশ্বাসের ভিত্তিতে কোনও কিছু মেনে নেননি তিনি। তাদেরও পুরোপুরি তাঁর শিক্ষা দেওয়া সত্য জানতে হবে এবং ধ্যানের সাহায্যে সেগুলোকে জীবন্ত অভিজ্ঞতায় পরিণত করতে হবে, যাতে যোগির ‘প্রত্যক্ষ জ্ঞান’ দিয়ে সেগুলো আত্মস্থ করতে পারে। সবার ওপরে, তাদের অবশ্যই অন্যের জন্যে বাঁচতে হবে। কেবল আলোকপ্রাপ্তির জন্যেই পবিত্র জীবনের উদ্ভাবন করা হয়নি। তাছাড়া, নিব্বানা এমন পুরস্কার নয় যে ভিক্ষু স্বার্থপরের মতো নিজের কাছে লুকিয়ে রাখবেন। তাঁদের অবশ্যই ‘মানুষের জন্যে, জনগণের কল্যাণ ও সুখের জন্যে, জগতের প্রতি সমবেদনা হতে এবং দেবতা ও মানুষের মঙ্গল ও শুভের জন্যে’[২২] ধম্ম পালন করতে হবে।
পরদিন সকালে বুদ্ধ ও আনন্দ শহরে খাবার ভিক্ষা করার পর বুদ্ধ ঘুরে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ সময় বেসালির দিকে চেয়ে রইলেন: শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছেন। এরপর ভানদাগামার পথ ধরেন ওঁরা। এই পর্যায় হতে বুদ্ধের ভ্রমণ যেন সত্য জগতের মানচিত্র হতে সরে যাচ্ছিল। ভানদাগামায় কিছুদিন অবস্থান করে সেখানকার ভিক্ষুদের নির্দেশনা দেওয়ার পর আনন্দকে নিয়ে ধীরে ধীরে উত্তরে হস্তিগামা, আম্বাগামা, জাম্বুগামা ও ভোগানাগামা (এগুলোর সবই কোনও চিহ্ন না রেখে হারিয়ে গেছে) হয়ে পাভায় এসে কুণ্ড নামের এক স্বর্ণকারের বাগিচায় অবস্থান গ্রহণ করলেন। বুদ্ধকে শ্রদ্ধা জানালেন কুণ্ড, মনোযোগ দিয়ে নির্দেশনা শুনলেন, তারপর এক অসাধারণ ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন তাঁকে যেখানে কিছু সুকারামাদ্দাভা (‘শূকরের নরম মাংস’) ছিল। খাবারটা আসলে কী ছিল নিশ্চিত নয় কেউঃ কোনও কোনও ভাষ্যকার বলেন এটা ছিল বাজারের শূকরের মাংস (বুদ্ধ কখনও তাঁর জন্যে বিশেষভাবে হত্যা করা কোনও প্রাণীর মাংস খাননি): অন্যরা যুক্তি দেখিয়েছেন, এটা হয় কুচিকুচি করে কাটা শূয়োরের মাংস বা শূয়োরের খাবার সুগন্ধী ব্যাঙের ছাতা ছিল। কারও মতে এটা ছিল বিশেষ ধরনের আরক। বুদ্ধ সেরাতে মারা গিয়ে পরিনিব্বানা লাভ করতে পারেন ভেবে কুণ্ড এ খাবার তাঁর জীবন অনির্দিষ্ট কাল প্রলম্বিত করবে বলে ভেবেছিলেন।[২৩] সে যাই হোক, বুদ্ধ সুকারামাদ্দাধা খাওয়ার জন্যে জোর করলেন; অন্য ভিক্ষুদের টেবিলের অন্যান্য খাবার খেতে বললেন। খাবার শেষে পর কুণ্ডকে তিনি বললেন অবশিষ্ট খাবরটুকু মাটি চাপা দিতে, যেহেতু আর কেউ–এমনকি দেবতাও নয়–এটা হজম করতে পারবে না। এটা কুণ্ডের রান্নার নৈপুণ্যের বিপরীত মূল্যায়ন হতে পারে। কিন্তু কোনও কোনও আধুনিক পণ্ডিত মত দিয়েছেন যে, বুদ্ধ বুঝতে পেরেছিলেন সুকারামাদ্দাভায় বিষ মেশানো হয়েছিল: তাঁরা বুদ্ধের দিক থেকে নিঃসঙ্গতা ও জায়গার দূরত্বকে বুদ্ধ ও সংঘের দূরত্বের চিহ্ন হিসাবে দেখেছেন এবং বিশ্বাস করেন যে দুজন বৃদ্ধ রাজার মতো তিনিও সহিংস মৃত্যু বরণ করেছেন।[২৪]
কিন্তু পালি টেক্সট এমনকি এই ভীতিকর সম্ভাবনা বিবেচনায়ও আনেনি I কুণ্ডকে খাবার মাটি চাপা দেওয়ার বুদ্ধের অনুরোধ অদ্ভুত ছিল। কিন্তু কিছুদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন তিনি। অচিরেই মারা যাবেন বলে প্রত্যাশিত ছিল। সেরাতে রক্তবমি শুরু করেন তিনি, তীব্র, যন্ত্রণায় আক্রান্ত হন, কিন্তু আবারও অসুস্থতা সামলে আনন্দকে নিয়ে কুশিনারার পথ ধরেন। এখন মাল্লা প্রজাতন্ত্রের সীমানায় ছিলেন তিনি। এখানকার অধিবাসীরা বুদ্ধের ধারণার প্রতি তেমন আগ্রহী ছিল বলে মনে হয় না। টেক্সট আমাদের বলছে, সন্ন্যাসীদের স্বাভাবিক দল ছিল তাঁর সঙ্গে, কিন্তু আনন্দ বাদে সংগঠনের কোনও প্রবীন সদস্য তাঁর সঙ্গে ছিলেন না। কুশিয়ানারার পথে ক্লান্ত হয়ে পড়েন বুদ্ধ, পানি খেতে চান। নদী স্থবির ও দুর্গন্ধময় হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধের পাত্র নিয়ে আনন্দ এগিয়ে যাওয়ামাত্র পানি স্বচ্ছ টলটলে হয়ে ওঠে। ধর্মগ্রন্থসমূহ শেষের এই দিনগুলোর মলিন নিঃসঙ্গতা চাপা দিতে এইসব ঘটনার প্রতি জোর দিয়েছে। আমরা জানতে পারি, যাত্রার শেষ পর্যায়ে একজন মাল্লিয় পথিককে দীক্ষা দেন বুদ্ধ। লোকটা মানানসইভাবে তার পুরোনো গুরু আলারা কালামের অনুসারী ছিল। বুদ্ধের মনোসংযোগের মান দেখে মানুষটি এত মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল যে সেখানেই সে ত্রিসীমা আশ্রয় নির্মাণ করে এবং বুদ্ধ ও আনন্দকে সোনার কাপড়ের দুটো জোব্বা উপহার দেয়। কিন্তু বুদ্ধ তাঁর জোব্বা পরার পর আনন্দ চেঁচিয়ে বলে উঠলেন যে তাঁর উজ্জ্বল চামড়ার তুলনায় ওটাকে একেবারেই মলিন লাগছে: বুদ্ধ ব্যাখ্যা করলেন যে এটা তিনি যে অচিরেই-কুশিনারায় পৌঁছার পর-চূড়ান্ত নিব্বানা লাভ করবেন সেই চিহ্ন। খানিক পরে আনন্দকে বললেন তাঁর মৃত্যুর জন্যে কেউ যেন কুণ্ডকে দায়ী না করে: পরিনিব্বানা লাভের আগে বুদ্ধকে শেষ খাদ্য যোগানো বিরাট পূণ্যের কাজ।[২৫]
এই পরিনিব্বান। আসলে কী? এটা কি স্রেফ বিলুপ্তি? যদি তাই হয়, তাহলে শূন্যতাকে কেন এমন মহৎ অর্জন হিসাবে দেখা হয়েছে? এই ‘চূড়ান্ত’ নিব্বানা বোধি রক্ষের নিচে বুদ্ধ যে প্রশান্তি লাভ করেছিলেন তার চেয়ে আলাদা হবে কেমন করে? স্মরণযোগ্য, ‘নিব্বানা’ শব্দটির মানে ‘শীতল হওয়া’ বা কোনও শিখার মতো ‘নিভে যাওয়া’। টেক্সট বর্তমান জীবনে নিব্বানা অর্জনের পরিভাষা হচ্ছে সা-উপদি-সেসা। একজন আরাহান্ত আকাঙ্ক্ষা, ঘৃণা ও অজ্ঞতার আগুন নিভিয়ে ফেলেছেন, কিন্তু এখনও তার মাঝে ‘জ্বালানি’র (উপদি) ‘অবশিষ্ট’ (সেসা) রয়ে গেছে, যতক্ষণ তিনি দেহে অবস্থান করছেন, মন আর ইন্দ্রিয় কাজে লাগাচ্ছেন ও আবেগ অনুভব করছেন আরও জ্বালানোর একটা সম্ভাবনা রয়ে গেছে। কিন্তু একজন আরাহান্ত যখন মারা যান এই খণ্ড আর জ্বলে উঠতে পারে না, ফলে নতুন অস্তিত্বের শিখা প্রজ্জ্বলিত করতে পারে না।[২৬] সুতরাং আরাহান্ত সামসারা হতে মুক্ত এবং নিব্বানার শান্তি ও প্রতিরক্ষায় পুরোপুরি নিমজ্জিত হতে পারেন।
কিন্তু তার মানে কী? আমরা দেখেছি, বুদ্ধ সব সময়ই নিব্বানার সংজ্ঞা দিতে অস্বীকার করেছেন। কারণ অনুভূতি ও মনের আওতার বাইরের এই অভিজ্ঞতাকে বর্ণনা করার মতো কোনও পরিভাষা আমাদের নেই। ঈশ্বর সম্পর্কে নেতিবাচক সুরে কথা বলে যেসব একেশ্বরবাদী তাদের মতো বুদ্ধ মাঝেমাঝে নিব্বানা কী নয় সেটাই ব্যাখ্যা করতে পছন্দ করতেন। শিষ্যদের তিনি জানিয়েছেন যে এটা একটা অবস্থা।
যেখানে জমিন বা পানি, আলো বা হাওয়া, অসীম বা স্থান কোনওটাই নেই; এটা কারণের অসীমতা নয় আবার পরম শূণ্যতাও নয়…এটা বর্তমান জগৎ বা ভিন্ন জগৎ নয়; এটা চন্দ্র ও সূর্য দুটোই।[২৭]
তার মানে এই নয় যে আসলেই ‘কিছু না’ বুঝিয়েছে এটা। আমরা দেখেছি, নিব্বানায় কোনও আরাহান্তের বিলুপ্তি ঘটার দাবি বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে ধর্মদ্রোহীতায় পরিণত হয়েছিল। তবে এটা সত্তার অতীত এক অস্তিত্ব। স্বার্থপরতা নেই বলে প্রশান্তিময়। আমরা যারা অনালোকিত, যাদের দিগন্ত এখনও অহমবাদে সংকীর্ণ, তারা এই অবস্থা কল্পনা করতে পারবে না। কিন্তু যারা অহমের মৃত্যু অর্জন করেছে, তারা জানে যে স্বার্থহীনতা শূন্যতা নয়। বুদ্ধ শিষ্যদের মনের অন্তস্তলের এই প্রশান্তিময় স্বর্গোদ্যান কী সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার প্রয়াসে নেতিবাচক ও ইতিবাচক পরিভাষার মিশ্রণ ঘটিয়েছেন নিব্বানা, বলেছেন তিনি, ‘লোভ, ঘৃণা ও বিভ্রমের নির্বাপন’; তৃতীয় মহান সত্যি; এটা ‘কলঙ্কহীন,’ অদুৰ্বল,’ ‘অভঙ্গুর,’ ‘অলঙ্ঘনীয়,’ ‘অহতাশ,’ ‘অনাক্রান্ত’ এবং ‘বৈরিতাহীন।’ এইসব বৈশিষ্ট্য জোর দেয় যে নিব্বানা আমরা জীবনে যেসব বিষয় অসহনীয় বলে আবিষ্কার করি তার সবই নাকচ করে। এটা নিশ্চিহ্নতার অবস্থা নয়; এটা ‘মৃত্যুহীন।’ কিন্তু নিব্বানা সম্পর্কে ইতিবাচক কথাও বলা যেতে পারে: এটা ‘সত্যি,’ ‘নিগূঢ়,’ ‘অপর পার,’ ‘চিরন্তন,’ ‘শান্তি, ‘ উৎকৃষ্ট লক্ষ্য,’ ‘নিরাপত্তা’ ‘মুক্তি,’ ‘স্বাধীনতা’, ‘দ্বীপ,’ ‘আশ্রয়,’ ‘পোতাশ্রয়, ‘ ‘শরণ,’ ‘ওপার।’[২৮] এটা দেবতা ও মানুষ উভয়ের পক্ষেই পরম শুভ। এক অনির্বচনীয় শান্তি ও সম্পূর্ণ নিরাপদ আশ্রয়। এইসব ইমেজের অনেকগুলোই ঈশ্বরকে বর্ণনা করার বেলায় একেশ্বরবাদীদের ব্যবহৃত শব্দের স্মারক।
প্রকৃতপক্ষে নিব্বানা অনেকাংশেই খোদ বুদ্ধের মতোই। মহায়না মতবাদের অনুসারী পরবর্তী কালের বৌদ্ধরা দাবি করবে, তিনি নিব্বানায় এমন ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছিলেন তাঁরা হয়ে পড়েছিলেন অবিচ্ছেদ্য। ঠিক ক্রিশ্চানরা যেমন মানুষ জেসাসকে নিয়ে চিন্তা করার সময় ঈশ্বর কেমন হতে পারেন উপলব্ধি করতে পারে, তেমনি বৌদ্ধরাও বুদ্ধকে এই অবস্থার মানবীয় রূপ হিসাবে দেখতে পায়। এমনকি তাঁর জীবনেই মানুষ এর আভাস লাভ করেছে। যে ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে কোনও শ্রেণীতে ফেলতে পারেননি, যেহেতু তিনি জাগতিক বা স্বর্গীয় শ্রেণীতে খাপ খাননি, তিনি অনুভব করেছেন যে নিব্বানার মতো বুদ্ধ ‘ভিন্ন কিছু।’ বুদ্ধ তাঁকে বলেছিলেন, তিনি হচ্ছেন ‘যে জেগে উঠেছে,’ এমন একজন মানুষ যিনি ইহজাগতিক মানুষের ভীতিকর, বেদনাময় সীমাবদ্ধতা ঝেড়ে ফেলে বাইরের কিছু অর্জন করেছেন। রাজা পাসেনেদিও বুদ্ধকে আশ্রয়, নিরাপত্তা ও বিশুদ্ধতার একটা স্থান হিসাবে দেখেছেন। গৃহ ত্যাগ করার পর তিনি আপন অন্তরে শান্তির এই নতুন অঞ্চল আবিষ্কার না করা পর্যন্ত মানবীয় প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করেছেন। কিন্তু তিনি অনন্য ছিলেন না। পবিত্র জীবনে গুরুত্বের সঙ্গে অংশগ্রহণকারী যে কেউ নিজের মাঝে এই স্বৰ্গীয় প্রশান্তি লাভ করতে পারে। পঁয়তাল্লিশ বছর অহমহীন মানুষ হিসাবে জীবন কাটিয়েছেন বুদ্ধ। সুতরাং, তিনি বেদনার সঙ্গে বসবাসে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু এখন জীবনের অন্তিম প্রান্তের দিকে যখন এগিয়ে যাচ্ছেন, বয়সের শেষ অসম্মানটুকুও ঝেড়ে ফেলবেন। তরুণ বয়সে লোভ ও বিভ্রমের কারণে জ্বলন্ত ‘জ্বালানি কাঠ,’ খণ্ড বহুদিন আগেই নির্বাপিত হয়েছে। এখন তা ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া যাবে। তিনি অপর পারে পৌঁছাতে যাচ্ছেন। তো দুর্বল কিন্তু আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অজানা ছোট শহরের দিকে এগিয়ে চললেন তিনি যেখানে পরিনিব্বনা লাভ করবেন।
বুদ্ধ ও আনন্দ, দুজন বৃদ্ধ ভিক্ষুদের মিছিলসহ হিরন্নবতী নদী পেরিয়ে কুশিনারা মুখী পথের এক শালবনে প্রবেশ করলেন। ততক্ষণে বেদনায় আক্রান্ত হয়েছেন বুদ্ধ। শুয়ে পড়লেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে ফুলে ফুলে ভরে উঠল শালবন, পাঁপড়ি ঝরাতে শুরু করল, যদিও সেটা ফুল ফোঁটার মৌসুম ছিল না। দেবতায় ভরে গেল জায়গাটা। বুদ্ধ বললেন, তাঁর শেষ বিজয় দেখতে এসেছেন তাঁরা। কিন্তু বুদ্ধকে বেশি সম্মান দিয়েছিল অনুসারীদের তিনি যে ধৰ্ম্ম এনে দিয়েছিলেন তার প্রতি তাদের আনুগত্য।
মৃত্যুপথযাত্রী বুদ্ধ তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সংক্রান্ত নির্দেশনা দান করলেন : তাঁর দেহভষ্মকে চক্কবত্তীর দেহভষ্মের মতো করে দেখতে হবে;মরদেহ কাপড়ে মুড়ে সুগন্ধী কাঠের আগুনে পোড়াতে হবে, তারপর দেহাবশেষ কোনও বৃহৎ নগরের প্রধান চত্বরে কবর দিতে হবে। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত বুদ্ধকে চক্কবত্তীর সাথে তুলনা করা হয়েছে এবং আলোকন লাভের পর জগতকে নিপীড়ন আগ্রাসনভিত্তিক ক্ষমতার ভিত্তির বিকল্প প্রস্তাব দিয়েছিল। অন্তে ্যষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা এই বিচিত্র বিপরীত বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করে। তরুণ গৌতম যখন মগধ ও কোসালায় আসেন তখন যে রাজাদের এমন ক্ষমতাধর মনে হয়েছিল, তাঁরা দুজনই শেষ হয়ে গেছেন। তাঁদের মৃত্যুর সহিংসতা ও নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছে যে রাজ্যগুলো স্বার্থপরতা, লোভ উচ্চাভিলাষ, হিংসা, ঘৃণা ও ধ্বংস নিয়ে চালিত হয়েছে। সেগুলো সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতিক অগ্রগতি বয়ে এনেছিল; উন্নয়নের ধারা তুলে ধরেছে ও বহু মানুষের উপকার সাধন করেছে। কিন্তু অন্য আরেক ধরনের জীবন ছিল যা এমন সহিংসভাবে নিজেকে চাপিয়ে দেয়নি, যা সত্তাকে ক্ষমতাবান করে তোলার জন্যে নিবেদিত ছিল না এবং যা আধুনিক নারী-পুরুষকে আরও সুখী, আরও মানবিক করে তুলেছে।
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন আনন্দের সহ্যের অতীত হয়ে পড়েছিল। শেষের এই দিনগুলোয় তাঁর কষ্ট আমাদের একজন অনালোকিত ও আরাহান্তকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা বিপুল দূরত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে বৌদ্ধ মতবাদ সম্পর্কে সবই জানতেন আনন্দ। কিন্তু এই জ্ঞান যোগির ‘প্রত্যক্ষ জ্ঞানের’ বিকল্প হতে পারে না। মনিবকে হারানোর বেদনা বোধ করার সময় কোনও কাজে আসবে না তা। সারিপুত্তের মৃত্যুর চেয়েও সীমাহীন খারাপ এই বেদনা। জাগতিক, যৌক্তিক মন দিয়ে ভোগান্তির মহান সত্য বুঝতে পেরেছিলেন তিনি। কিন্তু সেটা এমনভাবে আত্মস্থ করেননি যে সকল সত্তার সঙ্গে মিশে থাকবে। এখনও তিনি মেনে নিতে পারেননি যে সমস্ত কিছুই ক্ষণস্থায়ী, একসময় হারিয়ে যাবে। কারণ তিনি কুশলী যোগি ছিলেন না। তিনি এইসব মতবাদে ‘প্রবেশ’ করতে পারেননি, জীবিত বাস্তবতায় পরিণত করতে পারেননি এগুলোকে। যোগিদের মতো নিশ্চিন্ত বোধ করার বদলে কেবল তীব্র বেদনা বোধ করেছেন। আপন দেহভষ্ম সম্পর্কে বুদ্ধের নিরাসক্ত নির্দেশনা শোনার পর মনিবের বিছানার পাশ হতে উঠে গেলেন আনন্দ, পালালেন বনের অন্য একটা কুঁড়ের দিকে। দীর্ঘ সময় দেয়ালে মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদলেন। সম্পূর্ণ ব্যর্থ মনে হলো নিজেকে; ‘এখনও নবীশ রয়ে গেছি আমি, ‘ কাঁদলেন প্রবীন ভিক্ষু। ‘পবিত্র জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারিনি। আমার অনুসন্ধান অপূর্ণ রয়ে গেছে।’ আধ্যাত্মিক মহীরুহদের মাঝে জীবন কাটিয়েছেন তিনি। এখন কে তাঁকে সাহায্য করবে? কে তাঁকে নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবে? ‘আমার মনিব পরিনিব্বানা লাভ করতে যাচ্ছেন-আমরা দরদী মনিব, আমার প্রতি সবসময় দয়া দেখিয়েছেন যিনি।’
আনন্দের কান্নার সংবাদ পেয়ে তাঁকে ডেকে পাঠালেন বুদ্ধ। ‘যথেষ্ট হয়েছে, আনন্দ,’ বললেন তিনি। ‘বিষণ্ন হয়ো না। দুঃখ করো না।’ তিনি কি বারবার ব্যাখ্যা করেননি যে কোনও কিছুই স্থায়ী নয়, বরং বিচ্ছেদই জীবনের বিধান? ‘আর আনন্দ,’ উপসংহার টানলেন বুদ্ধ, ‘বহু বছর অন্তহীন ভালোবাসা ও দরদ দিয়ে আমার সেবা করেছ তুমি। আমার শারীরিক প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রেখেছ। তোমার কথা চিন্তায় সমর্থন যুগিয়েছে। তুমি পূণ্য অর্জন করেছ, আনন্দ। চেষ্টা চালিয়ে যাও। তুমিও শিগগিরই আলোকপ্রাপ্ত হবে।[২৯]
কিন্তু তখনও সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন আনন্দ। ‘প্রভু,’ চেঁচিয়ে উঠলেন তিনি, ‘এই ভয়ঙ্কর ছোট শহরে চূড়ান্ত বিশ্রামে যাবেন না। এখানে মাটির দেয়াল, এই বিধর্মী জংলী, বিরান এলাকায়।’ জীবনের অধিকাংশ সময় রাজাগহ, কোসাম্বি, সাবস্তি ও বারানসির মতো বিরাট শহরে কাটিয়েছেন বুদ্ধ। এখানে একাকী, এই অবিশ্বাসীদের মাঝে মৃত্যুবরণ না করে সেগুলোরই কোনও একটায় ফিরে অভিজাত অনুসারীদের মাঝে অনুসন্ধান শেষ করতে পারবেন না কেন? টেক্সট দেখায়, আদি সংঘ কুশিনারার অস্পষ্টতা ও তাদের গুরুর দূরে জঙ্গলে মারা যাওয়ার ব্যাপারে বিব্রত ছিল। কুশিনারা এককালে সমৃদ্ধ শহর ও একজন চক্কবত্তীর রাজধানী ছিল বলে আনন্দকে চাঙ্গা করার চেষ্টা করলেন বুদ্ধ। কিন্তু কুশিনারাকে বেছে নেওয়ার পেছনে বুদ্ধের নিশ্চয়ই গভীরতর কোনও কারণ ছিল। কোনও বৌদ্ধ অতীত অর্জনের ওপর নির্ভর করে থাকতে পারে না। সংঘকে সব সময় বিস্মৃত বিশ্বে সাহায্য পৌঁছে দিতে সামনে যেতে হবে। একজন বুদ্ধ কোনও আলোকিত মানুষের দৃষ্টিতে কুশিনারার মতো ছোট হতদরিদ্র শহরকে দেখবেন না। বহু বছর ধরে তিনি তাঁর মুক্ত সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে বাস্তবতাকে দেখার প্রশিক্ষণ দিয়ে এসেছেন। আমাদের অনেকেই সত্তার বোধ ফাঁপিয়ে তোলার জন্যে যে বাহ্যিক মর্যাদার ওপর নির্ভর করি তাঁর সেটা প্রয়োজন ছিল না। তথাগত হিসাবে তাঁর অহমবাদ ‘বিদায় নিয়েছিল।’ একজন বুদ্ধের নিজের কথা ভাববার সময় নেই, মৃত্যু শয্যায়ও না। একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অন্যের জন্যে বেঁচে ছিলেন তিনি। তাঁর বিজয়ের অংশী হতে কুশিনারার মাল্লয়ীদের বনে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এক পথচারী ভিক্ষুকেও নির্দেশনা দিতে সময় ব্যয় করেছেন। অন্য গোত্রের অনুসারী হলেও বুদ্ধের শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এই ভিক্ষু, বুদ্ধ অসুস্থ ও ক্লান্ত বলে আনন্দের প্রতিবাদ সত্ত্বেও।
অবশেষে আনন্দের দিকে ফিরলেন তিনি। স্বাভাবিক সহানুভূতি দিয়ে তাঁর চিন্তায় প্রবেশ করেছেন। ‘তুমি হয়তো ভাবছ, আনন্দ’: ‘গুরুর বাণী এখন অতীতের কথা: এখন আর আমাদের কোনও গুরু নেই।’ কিন্তু ব্যাপারটা এভাবে দেখা ঠিক হবে না। আমি বিদায় নেওয়ার পর তোমাকে যে ধম্ম আর অনুশীলন শিক্ষা দিয়েছি তাকেই গুরুর আসনে বসাও।[৩০] সবসময়ই অনুসারীদের তাঁর নয়, বরং ধম্মের মুখাপেক্ষী হতে বলেছেন তিনি। তিনি নিজে কখনও গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন না। অন্তিম যাত্রার সঙ্গী ভিক্ষুদের দিকে ফিরলেন এরপর। আরও একবার তাদের মনে করিয়ে দিলেন, ‘প্রতিটি জিনিস হারিয়ে যাবে। আন্তরিকতার সঙ্গে তোমাদের মুক্তির অন্বেষণ করো।[৩১]
অনুসারীদের শেষ পরামর্শ দেওয়ার পর অচেতন হয়ে পড়লেন বুদ্ধ। সন্ন্যাসীদের কেউ কেউ চেতনার উচ্চতর স্তর হয়ে তাঁর যাত্রা অনুসরণ করতে সক্ষম হলেন যা তিনি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় প্রায়ই করতেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতায় প্রভাবিত মন বিশিষ্ট কারও চেনা অবস্থার অতীতে চলে গিয়েছিলেন তিনি। দেবতাগণ আনন্দ-উল্লাস করার সময় কম্পিত হয়েছে পৃথিবী। আলোকপ্রাপ্ত হননি যেসব ভিক্ষু কেঁদেছেন তারা। এমন এক বিলুপ্তির অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন বুদ্ধ যা বৈপরীত্যমূলকভাবে সত্তার পরম স্তর ও মানুষের মোক্ষ।
দমকা হাওয়ায় নেভা শিখা
যেমন বিশ্রামে যায়, সংজ্ঞায়িত করা যায় না।
তেমনি আলোকপ্রাপ্তজন স্বার্থপরতা হতে মুক্ত
অবকাশে যান, সংজ্ঞায়িত করা যাবে না।
সকল কল্পনার অতীতে–
ভাষার শক্তির অতীতে গমন করেছেন।[৩২]
শেষ
তথ্যসূত্র
১. সাম্যত্তা নিকয়া, ৩: ২৫।
২. মাজহিমা নিকয়া, ৮৯।
৩. ভিক্ষু নানামোলি (অনু. ও সম্পা.), দ্য লাইফ অভ দ্য বুদ্ধা, অ্যাকর্ডিং টু দ্য পালি ক্যানন, কান্ডি, শ্রী লঙ্কা, ১৯৭২, ২৮৫ (ধারাভাষ্যে রয়েছে এই কাহিনী, লিপিতে নয়। )
৪. মাজহিমা নিকয়া, ১০৪।
৫. বিনয়া: কুলাভাগ্য, ৭: ২।
৬. প্রাগুক্ত, ৭: ৩।
৭. প্রাগুক্ত।
৮. প্রাগুক্ত।
৯. প্রাগুক্ত।
১০. প্রাগুক্ত।
১১. প্রাগুক্ত।
১২. প্রাগুক্ত, ৭: ৫।
১৩. দিঘা নিকয়া, ১৬।
১৪. প্রাগুক্ত।
১৫. প্রাগুক্ত।
১৬. প্রাগুক্ত।
১৭. প্রাগুক্ত, সাম্যত্তা নিকয়া, ৪৭: ৯।
১৮. দিঘা নিকয়া, ১৬; আঙুত্তারা নিয়া, ৮: ১০।
১৯. প্রাগুক্ত, ৪৭: ১৪।
২০. দিঘা নিকয়া, ১৬; আঙুত্তারা নিকয়া, ৮: ১০।
২১. দিঘা নিকয়া, ১৬।
২২. প্রাগুক্ত।
২৩. নানামোলি, লাইফ অভ বুদ্ধা, ৩৫৭-৫৮।
২৪. মাইকেল এডওয়ার্ডস, ইন দ্য ব্লোইং আউট অভ আ ফ্লেইম: দ্য ওঅর্ল্ড অভ দ্য বুদ্ধা অ্যান্ড দ্য ওঅর্ল্ড অভ ম্যান, লন্ডন, ১৯৭৬, ৪৫।
২৫. দিঘা নিকয়া ১৬।
২৬. রিচার্ড এফ, গমব্রিচ, থেরাভেদা বুদ্ধজম: আ সোশ্যাল হিস্ট্রি ফ্রম অ্যানশেন্ট বেনারেস টু মডার্ন কলোম্বো, লন্ডন, ও নিউ ইয়র্ক, ১৯৮৮, ৬৫-৬৯।
২৭. উদনা, ৮: ১।
২৮, সাম্যত্তা নিকয়া, ৪৩: ১-৪৪।
২৯. দিঘা নিকয়া, ১৬।
৩০. প্রাগুক্ত, আঙুত্তারা নিকয়া, ৭৬।
৩১. দিঘা নিকয়া, ১৬; আঙুত্তারা নিকয়া, ৪: ৭৬।
৩২. সুত্তা-নিপাতা, ৫: ৭।
৭. নির্ঘণ্ট
অহিংসা : ‘ক্ষতি না করা’: নতুন রাষ্ট্রসমূহের আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্যে উত্তর ভারতীয় বহু সাধুর গৃহীত নীতি
অকুসলা : আলোকনের প্রয়াসে বাধা সৃষ্টিকারী ‘অদক্ষ’ বা ‘অনুপযোগি’ অবস্থা।
অনাত্মা : ‘আত্মাহীন’: একটি নিত্য, স্থায়ী ও পৃথক ব্যক্তিত্ব অস্বীকারকারী মতবাদ।
আরাহান্ত : ‘সফল জন,’ যিনি নিব্বানা অর্জন করেছেন।
আরামা : বসতি স্থাপনের জন্যে বৌদ্ধ সংগঠনকে দান করা প্রমোদ-উদ্যান।
আসন : ঋজু পিঠ এবং পায়ের ওপর পা রেখে যোগ অনুশীলনের সঠিক ভঙ্গি। আবাসা: পল্লী বসতি, প্রায়শঃ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ বর্ষা মৌসুম অবকাশের জন্যে শূন্য হতে নিমার্ণ করতেন।
আত্মা : চিরন্তন অপরিবর্তনীয় সত্তা যোগি, সাধু আর সমক্ষ্য দর্শনের অনুসারীরা যার সন্ধান করেছেন। উপনিষদে একে ব্রহ্মার অনুরূপ বলে বিশ্বাস করা হয়েছে।
আয়তন : অগ্রসর যোগিদের অর্জিত ধ্যান মার্গ।
ভিক্ষু : ভিক্ষুক সন্ন্যাসী যিনি দৈনন্দিন খাবারের জন্যে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ান। নারীবাচক শব্দটি হচ্ছে ভিক্ষুনি: নান।
বোধিসত্তা : আলোকন প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়েছে এমন নারী বা পুরুষ। সংস্কৃত : বোধিসতবা।
ব্রহ্মা : বৈদিক ও উপনিষদ ধর্মে মহাবিশ্বের মৌলিক, পরম ও চরম নীতি।
ব্রাহ্মণ : উৎসর্গ ও বেদের পরম্পরা রক্ষার দায়িত্ব প্রাপ্ত আর্য সমাজের পুরোহিত গোত্রের সদস্য।
ব্রহ্মাচার্য : পবিত্র কৌমার্য জীবন: অলোকন ও বেদনা হতে মুক্তির অনুসন্ধান।
বুদ্ধ : আলোকপ্রাপ্ত বা জাগ্ৰত জন।
চক্কবর্ত্তী : ভারতীয় লোককথার বিশ্ব শাসক বা সর্বজনীন রাজা যিনি সমগ্র জগৎ শাসন করবেন এবং শক্তিবলে ন্যায় বিচার ও সঠিক পথ আনয়ন করবেন।
সেতো-বিমুক্তি : ‘মনের উন্মুক্তি’: আলোকন ও নিব্বানা অর্জনের সমার্থক।
ধম্ম : মূলত বস্তুর স্বাভাবিক অবস্থা, মূল; অস্তিত্বের মৌল বিধি; তারপর, ধর্মীয় সত্যি বিশেষ ধর্মীয় ব্যবস্থাও গড়ে তোলা মতবাদ ও অনুশীলন। সংস্কৃত: ধর্ম।
ধরণা : যোগ পরিভাষা: ‘মনোনিবেশ’। মনোছবির প্রক্রিয়া যেখানে যোগি আপন চেতনা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন।
দুঃখ : ‘কুটিল, ত্রুটিপূর্ণ, অসন্তোষজনক’: প্রায়শঃ স্রেফ ‘ভোগান্তি’ হিসাবে অনূদিত হয়।
একাগ্রতা : যোগে ‘নির্দিষ্ট বিন্দুতে’ মনোনিবেশ গৌতমী: গৌতমের গোত্রের যেকোনও নারী।
ইদ্ধি : বস্তুর ওপর মনের আধিপত্য। যোগের মাধ্যমে প্রাপ্ত ‘অলৌকিক ক্ষমতা’ যেমন শূন্যে ভাসা, বা ইচ্ছাশক্তির জোরে অবয়ব পরিবর্তন।
ঝানা : যোগ-মোহাবেশ: চারটি স্পষ্ট পর্যায়ক্রমে গম্ভীর হয়ে ওঠা একীভূত ভাবনার প্রবাহ। সংস্কৃত: ধ্যান।
জিনা : জৈনদের ব্যবহৃত বুদ্ধের সম্মানসূচক পদবী, বিজয়ী।
কম্ম : কাজ, কর্ম। সংস্কৃত: কর্মণ।
খণ্ড : স্তূপ, বাণ্ডিল, পিণ্ড;’ বুদ্ধের অনাত্মা মতবাদে মানব ব্যক্তিত্বের উপাদান। পাঁচটি ‘স্তূপ’ হচ্ছে দেহ, অনুভূতি, ধারণা, সংকল্প ও চেতনা।
ক্ষত্রিয় : আর্য সমাজে সরকার পরিচালনা ও প্রতিরক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত যোদ্ধা, অভিজাত, সামন্ত শ্ৰেণী।
কুসলা : আলোকনের জন্যে বৌদ্ধদের অনুসৃত মনের, হৃদয়ের ‘দক্ষ’ বা ‘উপযোগি’ অবস্থা।
নিব্বানা : ‘নির্বাপিত হওয়া,’ ‘বিলুপ্তি: সত্তার বিলুপ্তি যা বেদনা (দুঃখ) হতে আলোকন ও মুক্তি এনে দেয়। সংস্কৃত: নির্বানা।
নিকয়া : পালি ধর্মগ্রন্থের আলোচনার ‘সংকলন’।
নিয়ামা : যোগ ধ্যানের পূর্বশর্ত মনস্তাত্ত্বিক ও দৈহিক অনুশীলন।
পাবজ্জ্য : ‘অগ্রসর হওয়া’ সন্ন্যাসীর পবিত্র জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে জগৎ ত্যাগ করা। পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধদের সংঘভুক্তির প্রথম পর্যায়।
পালি : বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংকলনে ব্যবহৃত উত্তর ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষা।
পরিনিব্বানা : ‘চূড়ান্ত নিব্বানা’: মৃত্যুতে অর্জিত আলোকনপ্রাপ্ত জনের চূড়ান্ত বিশ্রাম, যেহেতু তিনি আর অন্য অস্তিত্বে জন্ম গ্রহণ করবেন না।
পতিমোক্ষ : ‘শপথ’: যে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রথম দিকের সন্ন্যাসীগণ ছয় বছর পরপর বৌদ্ধ ধৰ্ম্ম উচ্চারণ করার উদ্দেশে সমবেত হতেন। পরে, বুদ্ধের মৃত্যুর পর এটা সংগঠনের মঠাচারের আবৃত্তি ও অপরাধ স্বীকারের অনুষ্ঠানে পরিণত হয়। পাক্ষিক ভিত্তিকে অনুষ্ঠিত হতো।
প্রকৃতি : সামক্ষ্য দর্শনে প্রাকৃতিক জগৎ।
প্রাণায়াম : যোগের শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুশীলন যা ঘোর ও সুস্থতার একটা অবস্থা নিয়ে আসে।
প্রত্যাহার : যোগে ‘অনুভূতির প্রত্যাহার,’ কেবল বুদ্ধি দিয়ে কোনও বস্তু অনুধাবন করার ক্ষমতা।
পুরুসা : সামক্ষ্য দর্শনে সকল বস্তুকে আবৃত করে রাখা পরম আত্মা।
শাক্য মুনি : ‘শাক্য রাজ্যের সাধু,’ বুদ্ধকে দেওয়া পদবী।
সমাধি : যোগ-মনোসংযোগ; ধ্যান; আলোকপ্রাপ্তির অষ্টশীলেন একটি।
সামক্ষ্য : ‘পার্থক্যকরণ’: যোগের অনুরূপ একটি দর্শন, বিসিই দ্বিতীয় শতাব্দীতে কাপিলার সাধুগণ প্রথম প্রচার করেন।
সাম্মা সামবুদ্ধা : প্রতি ৩২,০০০ বছরে একবার মানব সমাজে আবির্ভূত আলোকনের শিক্ষক; সিদ্ধার্থ গৌতম আমাদের বর্তমান যুগের সাম্মা সামবুদ্ধা।
সামসারা : ‘অব্যাহত যাত্রা’: জন্ম ও মৃত্যুর চক্র, মানুষকে যা পরবর্তী জীবনে চালিত করে: জাগতিক জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব ও অস্থিরতা।
সংঘ : মূলত গোত্রীয় সংসদ, উত্তর ভারতের প্রাচীন রাজ্যসমূহের প্রাচীন শাসক গোষ্ঠী। পরবর্তীকালে নির্দিষ্ট গুরুর শিক্ষা দেওয়া ধম্মের প্রচারকারী গোত্র; সবশেষে, ভিক্ষুদের বৌদ্ধ সংগঠন।
সংখারা : ‘গঠন,’ কম্মের গঠনকারী উপাদানসমূহ যা পরবর্তী অস্তিত্বের আকার
নির্ধারণ করে।
সুত্তা : ধর্মীয় আলোচনা; সংস্কৃত: সূত্ৰা।
তানহা : ভোগান্তির সবচেয়ে শক্তিশালী কারণ ‘আকাঙ্ক্ষা’ বা ‘বাসনা’।
তপস : কৃচ্ছ্রতা সাধন: আত্ম-শুদ্ধি 1
তথাগত: ‘এভাবে বিদায় গ্রহণকারী।’ আলোকপ্রাপ্তির পর বুদ্ধকে দেওয়া উপাধি। অনেক সময় ‘আদর্শজন’ হিসাবে অনূদিত।
তিপিটতাকা : আক্ষরিকভাবে ‘তিনি ঝুড়ি,’ পালি লিপির তিনটি প্রধান বিভাগ।
উপাদান: ‘আঁকড়ে থাকা,’ সংশ্লিষ্টতা; শব্দগতভাবে উপাদি অর্থাৎ জ্বালানির সঙ্গে সম্পর্কিত।
উপসোথা : বৈদিক ঐতিহ্যে উপবাস ও সংযমের দিন।
উপনিষদ : বেদের অতিন্দ্রীয় ও আধ্যাত্মিকভাবে বোধগম্যতা গড়ে তোলা নিগূঢ় উপলব্ধি; পরবর্তী কালে হিন্দু ধর্মের ভিত্তি গড়ে তুলেছিল।
বাস্যা: জুন হতে সেপ্টেম্বর সময়কালে বর্ষা মৌসুমে অবকাশ।
বেদ : আর্য ধর্মীয় ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের উচ্চারিত ও ব্যাখ্যাকৃত অনুপ্রাণিত টেক্সট।
বিনয়া : বৌদ্ধ ব্যবস্থায় মঠ সংক্রান্ত আচরণ বিধি: তিপিটতাকার ‘তিনটি ঝুড়ি’র একটি।
বৈশ্য : আর্য ব্যবস্থার কৃষক ও পশুপালকদের তৃতীয় গোত্র।
বাসনা : মনের অবচেতন কর্মকাণ্ড।
ইয়ামা : যোগি ও সাধুদের অনুসৃত ‘নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ’ যাদের চুরি, মিথ্যাবলা যৌনমিলন, মাদক গ্রহণ বা অন্য প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া বা হত্যা করা নিষেধ।
যোগ : চেতনা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকল্প অবস্থার বিকাশে মনের শক্তি নিয়ন্ত্রণ করার অনুশীলন।
যোগি : যোগের অনুশীলনকারী।