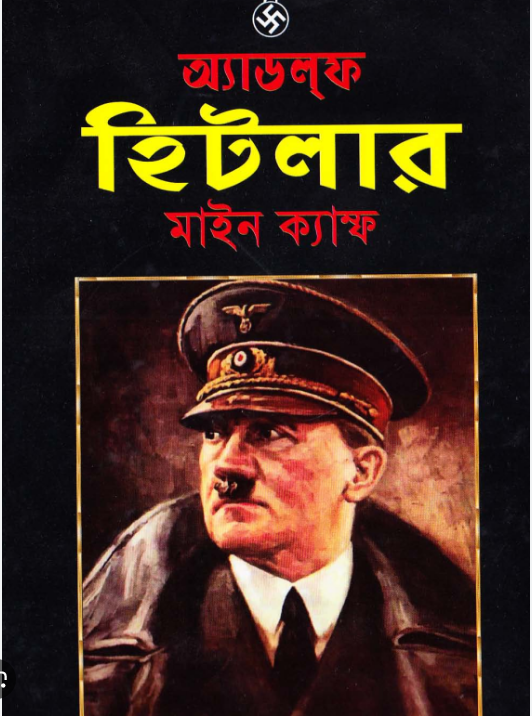- বইয়ের নামঃ মাইন ক্যাম্ফ
- লেখকের নামঃ অ্যাডলফ হিটলার
- প্রকাশনাঃ দি স্কাই পাবলিশার্স
- বিভাগসমূহঃ অনুবাদ বই
০১. ধূসর অতীত – মা বাবার সঙ্গে
মাইন ক্যাম্ফ (আমার সংগ্রাম)
মূল : অ্যাডলফ হিটলার। রূপান্তর : আক্কাস আলী। প্রকাশকাল : বইমেলা ২০১৩
লেখকের কথা
১৯২৪ সালের ১ এপ্রিল, মিউনিক গণ-আদালতের বিচারে লেখ্ নদীর তীরে ল্যান্ডবার্গের দুর্গে আমার কারাবাসের দিনগুলো শুরু হয়।
গত কয়েক বছরের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমের পর একটা কাজ করার মত সময় এ প্রথম আমার ভাগ্যে জোটে; অনেকেই আগে আমাকে অনুরোধ করেছে এবং আমি নিজেও ভেবেছি যে আমাদের সংগ্রামের পক্ষে এটা অত্যন্ত মূল্যবান। সুতরাং এ ভেবেই আমি এ বইটা লেখা শুরু করি, যার মূল উদ্দেশ্য শুধু সংগ্রামটাকেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া নয়, তাকে উন্নত করাও। তাই এ বই থেকে এমন অনেক কিছু শেখার আছে যা তৎকালীন পারিপার্শ্বিক লেখা বা প্রবন্ধ থেকে পাওয়া সম্ভব নয়।
আমি কিভাবে উন্নতির সোপান বেয়ে ওপরে উঠেছি, এ বইয়ের প্রথম এবং দ্বিতীয় অংশে তা বর্ণনা করেছি। শুধু তাই নয়; আমার সম্পর্কে ইহুদী সাংবাদিকরা যে কল্পিত অপপ্রচার করেছে, সেটা ধ্বংস করার সুযোগও এ বইয়ের মাধ্যমেই আমি পেয়েছি।
এ বই আমাকে দূরে সরিয়ে রাখবে না, বরং সংগ্রাম যাদের হৃদয়ের দাবি তাদের কাছাকাছি আমাকে পৌঁছে দেবে, তাদের জ্ঞান বাড়াতে সাহায্য করবে। আমি জানি যত লোককে মুখের কথায় কাজ করানো যায়, লেখার দ্বারা তা সম্ভব নয়। প্রতিটি সৎ এবং মহৎ সংগ্রাম পৃথিবীতে যা সংগঠিত হয়েছে, তা জন্ম নিয়েছে মহৎ বক্তার বক্তৃতা থেকে, কোন বড় লেখকের লেখা থেকে নয়।
যাহোক, ভণিতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের দৃঢ় হাতিয়ার হিসেবেও লেখাটা প্রয়োজন। সুতরাং এ বইটি তার ভিত্তিপ্রস্তর।
অ্যাডলফ হিটলার
দি ফোর্টেস
ল্যান্ডস্বার্গ লেখ্ নদীর তীরে
.
উৎসর্গ
১৯২৩ সালের ৯ নভেম্বর সাড়ে বারটার সময় ফেল্ড হেরেনহালের সামনে গণ-আদালতে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত এবং মিউকিনের সামরিক বাহিনী কর্তৃক তৎকালীন জনগণের উদ্ধারকার্যে ব্রতী হওয়ার দোষে যারা নিহত হয়েছেন :
অ্যালফার্থ ফেলিক্স, ব্যবসায়ী, জন্ম ৫ জুলাই, ১৯০১ সালে।
বাউরিড্যাল অ্যানড্রেস, টুপী প্রস্তুতকারক, জন্ম ৪ মে, ১৮৮৯ সাল।
ক্যাসেলা থিয়োডর, ব্যাঙ্ক কর্মচারি, জন্ম ৮ আগস্ট, ১৯৯০ সাল।
অ্যারলিক উইলহেম, ব্যাঙ্ক কর্মচারি, জন্ম ১৯ আগস্ট, ১৮৯৪ সাল।
ফাউষ্ট মার্টিন, ব্যাঙ্ক কর্মচারি, জন্ম ২৭ জানুয়ারি, ১৯০১ সাল।
হেথেনবার্গার আন্তু, তালা প্রস্তুতকারক, জন্ম ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯০২ সাল।
কর্ণে অস্কার, ব্যবসায়ী, জন ৪ জানুয়ারি, ১৮৭৫ সালে।
কুন কাইল, মুখ্য পরিচালক, জন্ম ২৬ জুলাই, ১৮৯৭ সাল।
লাফোর্স কার্ল, ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র, জন্ম ২৮ অক্টোবর, ১৯০৪ সাল।
নই বাউয়রে ফুর্ট, পরিচালক, জন্ম ১৬ আগস্ট, ১৯০৪ সাল।
ফোর্ডটেন থিয়োডর ভন্ ডার, উচ্চ প্রাদেশিক কোর্টের কাউন্সিলার, জন্ম ১৪ মে, ১৮৮৪ সাল।
রিকমাস জো, অবসরপ্রাপ্ত অশ্ববাহিনীর অধিনায়ক, জন্ম ৭ মে, ১৮৮৪ সাল।
সাউনার রিতার মাস্ক আরভিন ভন্, ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার, জন্ম ৯ জানুয়ারি, ১৮৮৪ সাল।
স্ট্রানস্কি লরেন্স রিটার্ন ভন, ইঞ্জিনিয়ার, জন্ম ১৪ মার্চ, ১৮৯৯ সাল।
উলফ উইলহেলম্ ব্যবসায়ী, জন্ম ১৯ অক্টোবর, ১৮৯৮ সাল।
তথাকথিত জাতীয়তাবাদী অফিসারবৃন্দ এ মৃত নায়কদের এক জায়গায় কবর দেওয়ার সুযোগটুকু পর্যন্ত দিতে অস্বীকার করে। সে কারণে আমি আমার লেখা এ বইটির প্রথম অংশ তাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলাম; যাতে সেসব শহীদ স্মৃতির চিরায়ত শক্তি আমাদের সংগ্রামী সৈনিকদের আলো দেখাতে পারে।
অ্যাডলফ হিটলার
দি ফোর্টেস্,
লেখ্ নদীর তীর, ল্যান্ডস্বার্গ
১৬ অক্টোবর, ১৯২৪ সাল।
.
০১. ধূসর অতীত
মা বাবার সঙ্গে
ইন নদীর তীরে ব্রুনাই গ্রামে জন্মেছিলাম বলে আজ নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করি। ব্রুনাই ছোট গঞ্জশহর; সাদামাঠা হলেও জায়গা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক দুটো প্রদেশের মাঝে। এ দুই প্রদেশের একত্রীকরণের জন্য যে কোন উপায়েই আমাদের সারাটা জীবন উৎসর্গ করা উচিত।
জার্মান এবং অস্ট্রিয়াকে একই পতাকাতলে নিয়ে আসতে হবে। হ্যাঁ, তা ছলে-বলে অথবা যে কোন রকমের কৌশল প্রয়োগ করে। যদিও অর্থনৈতিক দিক থেকে বিচার করলে অস্ট্রিয়াকে জার্মানির পতাকাতলে না আনাটাই উচিত। হয়তো বা চরম বোকামি। কারণ সেদিক থেকে উভয়েই চরম অসুবিধায় পড়বে। তবু একত্রিকরণ করা চাই, যে কোন মূল্যে; এবং উপায়ে। দুদেশের লোকের ধমনীতে যখন একই রক্ত প্রবাহিত, তখন তাদের সবাইকে এনে জার্মানির পতাকাতলে দাঁড় করাতে হবে। নিজেদের সন্তানেরা যদি একত্রে পাশাপাশি দাঁড়াতেই না পারে তবে বিদেশী রাষ্ট্র জয়ের চিন্তাটা নিছক বাতুলতা। যখন জার্মানরা নিজেদের রাষ্ট্রের ফসলে নিজেদের উদর পূর্তি করতে পারবে না, তখনই অন্য রাষ্ট্রের দিকে হাত বাড়ানো উচিত। অবশ্য লাঙলটাকে উল্টো করে তখন তরবারী হিসেবে তা ব্যবহার করতে হবে। যুদ্ধের সময় স্বজন হারানোর চোখের জলে উত্তরকালের জার্মানদের জন্য সৃষ্টি করবে দৈনন্দিন বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় রসদ রুটি।
সুতরাং নাউ ছোট্ট গঞ্জ শহর হলেও আমার কাছে তার গুরুত্ব অনেক বেশি। তাছাড়া ওই গঞ্জশহরটার ঐতিহাসিক একটা মূল্য আছে। যখন আমার পিতৃভূমি জার্মানি বিদেশীদের হাতে লাঞ্ছিত, চরম অবমাননায় নিমজ্জিত, তখন সেই দুর্যোগের দিনে জোহানস্ পাম, একজন বই বিক্রেতা দেশপ্রেমিককে এ ব্রুনাউয়ের মাটিতে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। তার দোষ? সে তার পিতৃভূমিকে ভালবেসেছিল। তবু মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত জোহানস্ পাম তার সঙ্গী সাথীদের নাম বলেনি। ফরাসীদের নিষ্ঠুর অত্যাচার সত্ত্বেও। এর ঠিক আগে এ একই কারণে ফরাসীরা হত্যা করেছে লিও শ্লাগেটারকে।
[১৯৭২ থেকে ১৮২৪ পর্যন্ত জার্মানি ফরাসীদের পদানত ছিল। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে হোয়েনলিভেনের যুদ্ধে অস্ট্রিয়াকে পরাজিত করে ফরাসীরা ব্যাভেরিয়া প্রদেশের রাজধানী মিউনিক শহর অধিকার করে। ১৮০৫ সালে নেপোলিয়ান ব্যাভেরিয়ার নির্বাচিত প্রতিনিধিকে রাজা করে একটা সর্তে। প্রতিটি যুদ্ধে তিরিশ হাজার সৈন্য দিয়ে ফরাসীদের সাহায্য করতে হবে। ব্যাভেরিয়াকে এভাবে ফরাসীরা সম্পূর্ণ কজা করে ফেলে। ১৮০৬ খ্রিস্টাব্দে এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটা বিজ্ঞপ্তি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয়। নাম— চরম অবমাননায় জার্মানি। যারা এ বিজ্ঞপ্তিটা প্রচার করতে সাহায্য করেছিল, নুরেমবার্গের পুস্তক বিক্রেতা জোহানস্ ফিলিপ তার মধ্যে অন্যতম। ব্যাভেরিয়ার পুলিশের এক গুপ্তচর ফরাসীদের খরবটা দেওয়ায় ফরাসীরা পামকে গ্রেপ্তার করে। বীভৎস অত্যাচার করেও জোহানসের কাছ থেকে বিজ্ঞপ্তিটার প্রকাশক এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের নাম জানতে না পেরে, লোক দেখানো বিচারের পর নেপোলিয়নের আদেশে ব্রুনাউয়ের মাটিতে গুলি করে তাকে হত্যা করা হয় ২৬ আগস্ট ১৮০৩ সালে। সেই জায়গাতে স্থাপিত জোহানসের স্ট্যাচুটা হিটলারকে খুব ছেলেবেলা থেকেই আকর্ষণ করত।
লিও শ্যাগেটারের ব্যাপারটাও অনেকটা জোহানস্ পামের মত। শ্যাগেটার ধর্মতত্ত্বের ছাত্র হয়েও ১৯১৪ সালে যুদ্ধে যোগদান করে। গোলন্দাজ বাহিনীতে কাজ করে আয়রন ক্রুশ পেয়েছিল। ১৯২৩ সালে ফরাসীরা যখন রুড় অঞ্চল আক্রমণ করে, তাদের প্রতিহত করার জন্য শ্লাগেটার বদ্ধপরিকর হয়। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মিলে একটা রেল ব্রীজ উড়িয়ে দেয়; যাতে ফরাসীরা রুড় অঞ্চল থেকে নিজের দেশে কয়লা সহজে না নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু একজন জার্মান গুপ্তচর ফরাসীদের কানে পুরো ব্যাপারটা তুলে দেওয়ায় শ্যাগেটারকে ফরাসীরা গ্রেপ্তার করে। অনেক অত্যাচারেও শ্যাগেটার মুখ খোলে না। একটা সঙ্গীর নামও ওর মুখ থেকে বের করতে অক্ষম হওয়ায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে ফরাসীরা। শ্যাগেটার প্রথম থেকেই পুরো দোষটা নিজের ঘাড়ে নিয়ে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়। অবশ্য পরে ওর সঙ্গীসাথীরা ধরা পড়ে। বিচারে তাদের জেল হয়। ১৯২৩ সালের ২৬ মে শ্লাগেটারকে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে এনে দাঁড় করানো হয়। এ সময়ে সভারি জার্মানির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হয়েও ব্যাপারটাতে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করে।
শ্যাগেটার রুড় প্রতিরোধের প্রধানতম শহীদ আর ন্যাশানাল সোশ্যালিস্ট মুভমেন্টের অন্যতম নায়ক হিসেবে অল্পদিনের মধ্যেই খ্যাতিলাভ করে। অল্প বয়স থেকেই শ্যাগেটার এর সদস্য ছিল। তার সদস্য নম্বর ছিল ৬১।]
ইন্ নদীর তীরের এ ছোট্ট গঞ্জশহর শহীদদের স্মৃতিতে পবিত্র। গত শতাব্দীর শেষের দিকে, আমার বাবা-মা এখানেই বসবাস করতে আসেন। বাবা পুরো দস্তুর সরকারি কর্মচারী ছিলেন। এবং তার কর্তব্যকর্ম পালনে এতটুকুও শৈথিল্য ছিল না। মা প্রাণপণে আগলে রাখতেন সংসারটাকে। ছেলেমেয়েদের সব সময় স্নেহমমতায় ঘিরে রাখতেন। কিন্তু ব্রুনাইয়ের স্মৃতি আমার মনের আয়নায় তত উজ্জ্বল নয়। কারণ কয়েক বছর পরেই বাবাকে সেই ইন্ নদীর তীরের গঞ্জশহর ছাড়তে হয়। ই উপত্যকার আরো নিচের দিকের শহর পাসুতে নতুন কর্মভার নিয়ে বাবা চলে আসেন। পাসু পুরোপুরি জার্মানির মধ্যে।
তৎকালে অস্ট্রিয়ার সরকারি কর্মচারীদের চাকরিতে ঘনঘন বদলি করা হত। অর্থাৎ যাযাবরের মত আজ এখানে কাল সেখানে। কিছুদিন পরেই বাবাকে বদলী করা হয় পাস থেকে লিনৎসে। এখানেই বাবা সরকারি কর্ম থেকে অবসর নেন। পেনসনের কটা টাকার ওপর ভরসা করে জীবন পার করতে হবে। অর্থাৎ, বৃদ্ধ হলেও পরিশ্রমের হাত থেকে রেহাই নেই।
আমার বাবা ছিলেন খুবই গরীব ঘরের ছেলে। ঠাকুরদার সম্পত্তি বলতে একমাত্র ছোট্ট একটা কুঠির। দারিদ্রতাই বোধহয় বাবাকে জন্ম থেকে চঞ্চল করে তুলেছিল। মাত্র তের বছর বয়সে একটা থলে কাঁধে ঝুলিয়ে তাই বাবা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন ভিয়েনার উদ্দেশ্যে। তিনটে মাত্ৰগালডেন পকেটে সম্বল। সতেরো বছর বয়সে অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করে বাবা কারিগর হন। কিন্তু ততদিনে জলমলে শহর ভিয়েনা বাবার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দিয়েছে। ছোটবেলায় যার একমাত্র স্বপ্ন ছিল গ্রামের গীর্জার ফাদার হওয়ার, সেই সব স্বপ্ন ততদিন মুছে গেছে। কারিগর হয়ে জীবনধারণের যে গ্লানি, তার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বাবা শুরু করেন অবিরাম পরিশ্রম। সরকারি চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা যে করেই হোক অর্জন করতে হবে। তেইশ বছর বয়সে বাবা সেই যোগ্যতা অর্জন করে নিজের গ্রামে ফিরে আসেন। দেহমনের সমস্ত শক্তি দিয়েও বাবা নিজের জীবনের প্রতিজ্ঞা এভাবে পূরণ করেছিলেন।
জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করলেও গ্রামে বাবা তখন তো সম্পূর্ণ অপরিচিত। অতটুকু বয়সে গ্রাম ত্যাগ করে চলে যাওয়াতে গ্রামের কেউই আর বাবাকে স্মরণে রাখেনি। নিজের গ্রামেই বাবা যেন প্রবাসী ছিলেন।
অবশেষে পঁয়ষট্টি বছর বয়সে বাবা চাকরি থেকে অবসর নেন। কিন্তু এখন কি করবেন? জীবনে একটা দিনও তার কুঁড়েমিতে কাটেনি। সত্যি বলতে কি আলস্য শব্দটাই বাবার অভিধানে ছিল না। সুতরাং অনেক চিন্তা ভাবনার পর আপার অস্ট্রিয়ার ছোট বাণিজ্য শহর লামবাখের শহরতলীতে বাবা পুরনো একটা ফার্ম কিনে চাষবাস শুরু করেন। অর্থাৎ এত বছর বিভিন্ন ঘাটে ঘুরে শেষমেষ পিতামহের পেশাকে বেছে নেন।
ঠিক এ সময়েই আমার জীবনের কিছুটা মোড় ঘোরে। লামবাখের উদার প্রান্তর, বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে হেঁটে স্কুলে যাওয়া। কয়েকটা বেপরোয়া ছেলের সঙ্গেও এ সময় বন্ধুত্ব হয়। অবশ্য সেই কারণে মা কিছুটা উদ্বিগ্ন ছিলেন। ছুটি কাটানো সম্পর্কে আমি বরাবরই উদাসীন। অর্থাৎ সংসারের আরো দশটা ছেলের মত নিরুপদ্রবে ছুটি কাটানো আমার ধাতে ছিল না। বন্ধুদের সঙ্গে তাই নিয়ে জোর বিতর্ক লেগেই থাকত, যেটা ভবিষ্যতে আমার বক্তৃতা দেওয়ার অভ্যাসে পরিণত করে। লামবাখে থাকাকালীন আমার আরেকটা অভ্যাস গড়ে ওঠে। নিয়মিত সেখানকার গির্জায় গিয়ে ধর্মীয় সঙ্গীত অথবা আলোচনায় অংশ নিয়ে দেখেছিলাম কী করে মানুষের অনুভূতিশীল মনটাকে অনুভূতির চরমে নিয়ে যেতে হয়। অবশ্যই বাবার নিজের জীবনেও ছোটবেলায় আকাক্ষা ছিল নিজের গ্রামের চার্চের ফাদার হওয়ার। আমার জীবনে আমিও সেটাকেই জীবনের সবচেয়ে কাম্য বলে ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু বাবা কিছুতেই তাতে সায় দেননি। অর্থাৎ আমার ছেলেমানুষী কল্পনাকে বাবা কোনরকম আমল দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। আমার জীবনের সংঘাত বোধহয় এ অধ্যায়েই শুরু হয়।
বাবার বইপত্রগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে কয়েকটা বইয়ের বিজ্ঞাপন আমার নজরে আসে। সেই বইগুলো সবই মিলিটারী বিষয় সংক্রান্ত। বিশেষ করে একটা বই তো আমাকে ভীষণভাবে আক্রমণ করে। বইটি জনপ্রিয় ফ্রাংকো-জার্মান যুদ্ধের ইতিহাস ১৮৭০-৭১। দুটো পর্বে লেখা বইটি। চিত্রিত। যুদ্ধের তথ্যপঞ্জীতে ঠাসা। এ বইটি পড়তে আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দ পেতাম। আর এ বইটি পড়েই কতগুলো প্রশ্ন আমার মনে জেগে ওঠে। মনের ভেতরে প্রচণ্ড আলোড়ন এনে দেয়। যুদ্ধ সংক্রান্ত যা কিছু পেতাম, সেই বয়স থেকেই তা গোগ্রাসে গিলতে শুরু করি। কিন্তু যুদ্ধ বিষয়ক এত বই পড়া সত্ত্বেও ফ্রাংকো–জার্মান বইটিই আমাকে বেশি ভাবিয়ে তোলে। তার মানে যে সব জার্মান সেই ১৮৭০-৭১ সালের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল আর যারা অংশ নেয়নি, উভয়পক্ষই জার্মান হওয়া সত্ত্বেও কি তাদের মধ্যে কিছু ফারাক ছিল? আর যদি না থাকে তবে কেন তারা একই পতাকার নিচে এসে জমায়েত হল না। অস্ট্রিয়া-ই বা কেন সেই যুদ্ধে অংশ নিল না। আমার বাবাও সে যুদ্ধে যায়নি। তা হলে কি আমরা, আর অন্যান্য জার্মান যারা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল তারা এক নয়? এসব সূচীমুখ জিজ্ঞাসাগুলো আমার ছোট মস্তিষ্কটাকে চঞ্চল করে তুলল। অনেককে জিজ্ঞাসা করে বুঝলাম যে সব জার্মান সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়নি, তারা বিসমার্কের সাম্রাজ্যের মধ্যে বাস করত না। অবশ্য তবু বিষয়টা ঠিক আমার স্পষ্ট হল না।
আমার ধাত দেখে বিশেষ করে মর্জি বুঝে বাবা ঠিক করলেন পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করে আমার জীবনে কিছু হবে না। আর সেই কারণেই হয়ত বা জিমনাসিয়াম স্কুলে আমার বুদ্ধিবৃত্তির সঠিক বিকাশ হচ্ছে না। বরং পেশাগত স্কুলই আমার পক্ষে সঠিক। বিশেষ করে ড্রইংয়ের প্রতি আমার ছোটবেলা থেকে ঝোক বাবাকে তার মনস্থির করতে সাহায্য করে। অস্ট্রিয়ান জিমনাসিয়াম স্কুলে ড্রইংটাকে বিশেষভাবে অবহেলা করা হয়। উপরন্তু নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা দেখেছিলেন পরবর্তী জীবনে এ পুঁথিগত বিদ্যা কোন কাজেই আসে না। সুতরাং তার কাছে স্বভাবতই এ বিদ্যার কোন দামও ছিল না। অবচেতন মনে বাবা হয়তো বা আমাকে সরকারি কর্মচারী হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন বলা বোধহয় ভুল হবে, বাবা একরকম মনস্থির করেই ফেলেছিলেন যে আমাকে যে করে হোক সরকারি কর্মচারী করবেন। আসলে যে দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে তিনি নিজেকে সরকারি চাকরির যোগ্য করে তুলেছিলেন, সেটাই বাবাকে আরও বেশি প্রত্যয় এনে দিয়েছিল যে ছেলে নিশ্চয়ই তার পথে চলবে। বরং সরকারি চাকরিতে তার থেকেও একধাপ ওপরে উঠবে।
কিন্তু বাবা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি যে তার প্রস্তাব আমি অগ্রাহ্য করব। আসলে বাবা যেটাকে জীবনের সবকিছু প্রাপ্তি বলে ধরে নিয়েছিলেন, আমার কাছে সেটা কিছু নাও তো হতে পারে। বাবার চিন্তাধারা সহজ সরল এবং স্বচ্ছ। আসলে বেঁচে থাকার জন্য যে নিদারুণ সগ্রাম বাবাকে করতে হয়েছে, সেটাই তাকে ডিটেটর করে তুলেছিল। সুতরাং তার মতামতের কাছে জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এ বয়সের ছেলের মতামতের কতটুকুই বা মূল্য থাকতে পারে। বিশেষ করে আগামী ভবিষ্যতের পথ বেছে নেওয়ার ব্যাপারে।
কিন্তু তবু তিনি পারলেন না। আমারও তখন জেদ চেপে গেছে। এগারো বছর বয়সে জীবনে সেই প্রথম বাবার মতামতকে অগ্রাহ্য করলাম। ভয় অথবা স্নেহ কিছুই আমাকে আমার সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারে না। বাবার তুলে ধরা রঙিন ছবি আকর্ষণ করা দূরে থাক, আমাকে আরও বেশি বিদ্রোহী করে তোলে। সারাজীবন টুলে বসে দরখাস্ত সাজিয়ে আলমারীতে তুলে রাখা আর যার দ্বারা হোক আমার দ্বারা কিছুতেই সম্ভব নয়।
সহজেই অনুমেয় চলতি পথে ভাল ছেলে বলতে যা বোঝায় আমি তা ছিলাম না। সুতরাং কী ধরনের চিন্তার মেঘ আমার মনের আকাশে আনাগোনা করতে পারে! স্কুলের দেওয়া পড়াশোনা অতি অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করে আমার হাতে প্রচুর সময় থাকত। যেগুলো আমি চার দেওয়ালে বন্দী না থেকে উদার প্রান্তরের খোলা হাওয়ায় ঘুরে বেড়িয়ে বেহিসেবী খরচা করতাম। আজ যখন রাজনৈতিক বিরুদ্ধবাদীর দল আমার ব্যক্তিগত জীবনে উকি-ঝুঁকি দিয়ে প্রমাণ করতে চেষ্টা করে যে আমার ছেলেবেলা কত রকমের চালাকির মধ্যে দিয়ে কেটেছে, আমার তখন হাসি পায়। সত্যি বলতে কি আমার ছোটবেলার সুখস্মৃতি আজও আমাকে এগিয়ে যাবার প্রেরণা দেয়। বর্তমানের জটিল জগত থেকে সেদিনের কথা ভেবে মুহূর্তের জন্য হলেও যেন মুক্তি পাই।
পেশাগত স্কুলে ভর্তি হয়েও আমার দিনগুলোর পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু আরেক ধরনের দ্বন্দ্ব এসে মনটাকে জুড়ে বসে।
যতদিন বাবা আমাকে সরকারি কর্মচারী করে গড়ে তুলতে চেয়েছেন, ততদিন পর্যন্ত মনের দিক থেকে দ্বন্দ্বটা সোজা ছিল। অন্তত আমার দিক থেকে সরকারি চাকরি করব না–এ প্রতিজ্ঞাটাই এদিক থেকে মনের মুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু যখন স্থির করলাম যে আমি কী করতে চাই, তখনই চরম মানসিক দ্বন্দ্বে ভুগতে শুরু করি। বিশেষ করে বাবার কাছে তা উপস্থিত করতে। তখন আমার বয়স বারো। কি করে বলতে পারব না, তবে সেই বয়সেই মনস্থির করে ফেলেছি যে আমাকে শিল্পী হতেই হবে। হতে পারে ড্রইংয়ে আমার হাত পাকা ছিল বলেই ভেবেছিলাম শিল্পী হওয়াই আমার পক্ষে উপযুক্ত কাজ। কিন্তু বাবাকে বলি কি করে? যাহোক মনের দিক থেকে প্রস্তুত হয়ে নিয়ে বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম সব। আমি শিল্পী হতে চাই।
—তুমি শিল্পী হতে চাও? মানে? বাবা বিস্ময়ে বিমূঢ়।
বাবার তখন পর্যন্ত দৃঢ় সন্দেহ যে সত্যি আমি প্রকৃতিস্থ কিনা। বাবা তখনো ভাবছেন— আমার কথা ঠিক বুঝতে পারেননি অথবা ভুল শুনছেন। কিন্তু আমি যখন পুরো ব্যাপারটা বিস্তারিত খুলে বললাম, বাবা প্রথমে গম্ভীর হয়ে গেলেন। তারপর তার চরিত্র অনুসারে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করলেন। বাবার সোজাসুজি মতামত, এ হতে পারে না। হওয়া সম্ভব নয়।
—না, আমি বেঁচে থাকতে তা হতে পারে না।
স্বাভাবিকভাবে পিতার চরিত্রের কিছুটা যেমন ছেলের চরিত্রেও বর্তায়, তাই তার চারিত্রিক দৃঢ়তা জন্ম থেকে আমিও কিছুটা পেয়েছিলাম। আমিও প্রত্যয়ের সঙ্গে বাবার কথার প্রতিবাদ করি, আমাকে যেমন করে থোক শিল্পী হতেই হবে।
সুতরাং পরিস্থিতিটা বেশ ঘোরালো এবং জটিল হয়ে ওঠে। বৃদ্ধ দ্রলোক আমার ওপরে প্রচণ্ড রেগে গেলেও আমি বাবাকে ভালবাসতাম। বাবা আমাকে শিল্পী হতে যত বাধা দিতে লাগলেন, আমিও মনস্থির করলাম যে এছাড়া অন্য কোনরকম পড়াশোনা করব না। শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা রীতিমত টানাপোড়ানের হয়ে ওঠে। আমি নীরবে আমার পথ বেছে নিয়ে ঠিক করি যে পেশাগত স্কুলের পড়াশোনায় একেবারে মন দেব না। তাহলেই বাবাকে বাধ্য হয়ে আমার মতে মত দিতে হবে।
অবশ্য জানি না অংক ঠিক ছিল কিনা। কিন্তু আমার স্কুলের অমনোযোগিতা দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আসলে স্কুলে যে বিষয়ে আমার আকর্ষণ ছিল, অথবা ভাবতাম ভবিষ্যতে শিল্পী হতে গেলে কাজে লাগবে সেটাতেই শুধু মন দিতাম। আর বাকিগুলো স্রেফ বাদ। সুতরাং স্কুলের ফলাফলও সেই ধরনের হল। একটা বিষয়ে হয়ত বা খুব ভাল নম্বর পেলাম, আরেকটাতে আবার সাধারণ মানের চেয়েও নিচে। বিশেষ করে ভুগোল আর ইতিহাসে আকর্ষণ আমার বরাবরের।
এত বছর পরেও পেছনে ফিরে তাকালে দুটো জিনিস বুঝতে পারি। প্রথমত সেই বয়সেই আমি প্রচণ্ড রকমের জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠি; দ্বিতীয়ত তখনই ইতিহাসের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হই।
পুরনো অস্ট্রিয়ার অধিবাসীরা তখন মিশ্রিত জাত। বিশেষ করে ফ্রাংকো-জার্মান যুদ্ধের বিজয়ী জার্মানরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ না-কারী জার্মানদের হেয় নজরে দেখত। ভাবত যুদ্ধ করার উপযুক্ত ওরা নয়। আর সেই কারণেই সীমান্তের অপর পারের জার্মানদের সঙ্গে জার্মানির অব্যন্তরীণ জার্মানরা কোনরকম যোগাযোগ রাখত না।
জার্মান রাষ্ট্রের জার্মানরা একবার ভেবেও দেখেনি যে অস্ট্রিয়ার জার্মানরা যদি নিজেদের সত্যিকারের জার্মান বলে না ভাবত তবে কখনই বাহান্ন মিলিয়ান জার্মান ‘আমরা বলতে পারতাম না। ব্যাপারটা এতাই স্পষ্ট যে অনেক জার্মান নাগরিক জার্মান রাষ্ট্রের ভেতরে থেকেও অস্ট্রিয়াকে জার্মানির একটা অংশ বলে ভাবত। যাহোক, পূর্ব সীমান্ত অর্থাৎ জার্মান অস্ট্রিয়ার দশ মিলিয়ান অধিবাসী নিজেদের জার্মান বলেই মনে প্রাণে জানত। জার্মানির অভ্যন্তরের খুব অল্প জার্মানই জানত কত কষ্টে এ দশ মিলিয়ান জার্মান তাদের নিজস্ব জার্মান ভাষা, সংস্কৃতি, স্কুল ইত্যাদিকে বাঁচিয়ে রেখেছে।
আজকে যখন জার্মান জাতির একটা বিরাট অংশ বিদেশী শাসকের পদানত হয়ে মাতৃভাষার অধিকারের জন্য মরণপণ যুদ্ধ করে চলেছে, শুধু তখনই জার্মানির ভেতরকার জার্মানরা উপলব্ধি করেছে যে সত্যিকারের সংস্কৃতির জন্য, নিজেদের ভাষা রক্ষার জন্য, অস্ট্রিয়ার জার্মানরা কতখানি বদ্ধপরিকর। আর বর্তমানে হয়ত তারা এ-ও বুঝতে পারছে বিদেশী পদানত হয়ে নিজেদের সংস্কৃতি এবং মাতৃভাষাকে বাঁচিয়ে রাখা কতখানি কষ্টকর।
সব জায়গায় এসব ব্যাপারে যা হয়ে থাকে অস্ট্রিয়াতে তার ব্যতিক্রম হবে কেন। এ মাতৃভাষাকে বাঁচিয়ে রাখার ব্যাপারে তিনটি দল, পুরোপুরি সক্রিয়, একদল যারা মাতৃভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে, এগিয়ে নিয়ে যেতে, জীবনপণ করেছে; আরেকদল যারা সুবিধেবাদী; আর তৃতীয় দল হল বিশ্বাসঘাতক জুডাস। বিশেষ করে স্কুলগুলোকে কেন্দ্র করেই ব্যাপারটা চরমে ওঠে। আসলে আজকের চারাগাছগুলোই তো সব ভবিষ্যতের মহীরূহ। তাদের অপরিণত মস্তিষ্কে যেন তেন প্রকারে জিনিসটা গেঁথে দিতে হবে। তাহলেই কেল্লা ফতে। সুতরাং স্কুলে স্কুলে জার্মান শিশুদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেওয়া শুরু হয়ে যায়, জার্মান ছেলেরা ভুলে যেও না যে তোমাদের ধমনীতে জার্মান রক্ত প্রবাহিত। জার্মান মেয়েরা ভুলে যেন না যায় ভবিষ্যতে জার্মান সন্তান তোমরা গর্ভে ধারণ করবে, ইত্যাদি।
সমস্ত ব্যাপারটাতে আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া যায়। জার্মান ছেলেরা অজার্মান গান গাইতে আপত্তি করে, নিষিদ্ধ জার্মান রাজের ছাপ মারা পোশাক পরতে শুরু করে দেয়। অজার্মান শিক্ষকদের কাছে পড়া পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়। এমন কি জল-খাবারের পয়সা বাঁচিয়ে পর্যন্ত বড়দের হাতে তুলে দেয় যাতে এ সংগ্রামকে আরো বেশি জোরদার করা যায়, এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এর জন্য যে কোন রকম দৈহিক শাস্তি ওরা হাসিমুখেই বরণ করে নিত। এভাবে সেই যুদ্ধে অতি অল্প বয়সে আমি জড়িয়ে পড়লাম। সাউথ ফ্রন্টিয়ার লীগ অথবা স্কুল লীগের জামায়েতে আমরা গমের শিষ ছাপ মারা কালো-লাল সোনালী রঙের জামা পরে দলের প্রতি আমাদের বিশ্বস্ততা দেখাতাম। আমরা পরস্পরকে অভ্যর্থনা করতাম হাইল’ শব্দটা উচ্চারণ করে। অস্ট্রিয়ার জাতীয় সঙ্গীতের বদলে এসব জমায়েতে আমরা জার্মান জাতীয় সঙ্গীত, ডয়েচল্যান্ড ইবার আলেয় অর্থাৎ সবার ওপরে জার্মানি— গাইতাম। এ সবের জন্য কোনরকম শাস্তি বা জরিমানা আমরা গায়েই মাখতাম না। যে সময়ে একদল শিশু জাতীয়তাবাদী মন্ত্রে রীতিমত দীক্ষিত ও উৎসর্গীকৃত তখন অস্ট্রিয়ার লোকেরা নিজেদের ভাষা ছাড়া জাতীয়তাবোধ বলতে আর কিছুই বুঝত না।
এসব ঘটনাগুলো আমাকে অত্যন্ত দ্রুতবেগে জাতীয়তাবাদীর দিকে টেনে নিয়ে যায়। তখন আমার বয়স পনেরো বছর। কিন্তু এ ধরনের কাজে আমার সেই সময়েই রীতিমত উৎসাহ। জীবনের স্বাদ পেয়ে গেছি। যারা সেই সময়ের পৃথিবীর খবর জানে না অথবা হাববুর্গ শাসক সম্প্রদায় সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের পক্ষে ব্যাপারটা বোঝা সম্ভব নয়।
ইতিহাসের মধ্যে বিশ্ব ইতিহাসটাই বিশেষভাবে অস্ট্রিয়ার স্কুলে পড়ানো হত। অস্ট্রিয়ার নিজস্ব ইতিহাস খুবই সামান্য। সত্যি বলতে কি অস্ট্রিয়ার ভাগ্য জার্মানির উন্নতি বা অস্তিত্বের সঙ্গে একসুত্রে বাঁধা ছিল। সুতরাং অস্ট্রিয়ার নিজস্ব ইতিহাস বলতে প্রায় কিছুই ছিল না।
আগেকার সমাজের (যখন দ্বিতীয় ফ্রান্সিস পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের জার্মান অধীশ্বর রূপে নেপোলিয়ানের আদেশে নির্বাচিত হন, তখন তার মুকুট এবং রাজদণ্ড রাজার প্রতিভু স্বরূপ ভিয়েনায় রক্ষিত হয়। এ জিনিসগুলো জাতীয়তাবাদী জার্মানদের উদ্বুদ্ধ করতে ঠিক ম্যাজিকের মত কাজ করেছিল।
১৯১৮ সালে হাববুর্গ সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেলে অস্ট্রিয়ার জার্মানরা অনেক চেষ্টা করে ফাদারল্যান্ড অর্থাৎ পিতৃভূমি জার্মানির সঙ্গে মিলিত হওয়ার। সেই লক্ষ লক্ষ অস্ট্রিয়ার জার্মানদের নিজের পিতৃভূমিতে ফেরার জন্য যে আকুল ক্রন্দন উঠেছিল, একমাত্র ইতিহাসের বুকে কান পেতে শোনা ছাড়া তার আর কোন উপায় নেই। কেউ বুঝতেও পারবে না সেইসময় অস্ট্রিয়ার প্রতিটি জার্মান কী চরম হতাশার মধ্যে দিয়ে নিজেদের দিনগুলো পাড়ি দিয়েছে। সে গভীর ক্ষতের দাগ এখনো পর্যন্ত অস্ট্রিয়ার জার্মানদের মন থেকে মুছে যায়নি।
স্কুলে বিশ্ব ইতিহাস যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হত, তা মোটেই উপযুক্ত নয়। মুষ্টিমেয় শিক্ষকই উপলব্ধি করতে পারত, শুকনো কটা দিন, তারিখ আর পঞ্জীর মধ্যে আবদ্ধ যে ইতিহাস, সেটা জাতির ইতিহাস নয়। কবে কোথায় যুদ্ধ হয়েছে, কোন্ মার্শাল কত তারিখে মারা গেছে, অথবা কোন দিনে কার মাথার কোথার রাজমুকুট চড়েছে, এসব খবরাখবর একটা জাতির ইতিহাসে কতটুকু মূল্য?
ইতিহাসের অর্থ হল কোন বিশেষ ঘটনা কেন এবং কিভাবে একটা জাতির জীবনের মোড় ঘুরিয়ে ছিল সেইটাকে জানা। আর ইতিহাস পড়া উচিত— বিশেষ দরকারী জিনিসটাকে মনে রাখা, অদরকারী বিষয়টা ভুলে যাওয়া।
সম্ভবত এ সময়েই আমার ভবিষ্যৎ আমি স্থির করে ফেলি। তার জন্য যার কাছে আমি সম্পূর্ণ ঋণী তিনি হলেন আমার স্কুলের শিক্ষক, ডক্টর লিওপোন্ড পোয়েটি। লিৎজ স্কুলের। যে গুণগুলোর সমন্বয় ঘটলে সত্যিকারের ইতিহাসের শিক্ষক হওয়া যায়, তার মধ্যে সেইগুলোর যেন মণিকাঞ্চন যোগ ঘটেছিল। বয়সে বৃদ্ধ, দেখলে বোঝার উপায় নেই যে এত দয়ালু হৃদয়ের মানুষ। চমৎকার বলার ক্ষমতা। কথার মধ্য দিয়ে যেন হাজার বছর পেছনে আমাদের নিয়ে যেতেন। নিজের ভেতরকার উৎসাহটাকে ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর। পড়াশোনার সময়ে বর্তমানকে ভুলিয়ে দিয়ে আমাদের নিয়ে যেতেন সুদূর এক ধূসর অতীতে। মন্ত্রের মত। সেই পুরনো দিনের ইতিহাসের ঘটনার মিছিল ওর বলার ভঙ্গিতে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠতো। তারা যেন কথা বলত। আমাদের সঙ্গে নিয়েই তিনি সেই ইতিহাসের রাজ্যে বিচরণ করতেন। ইতিহাসের উপমাও ইতিহাস থেকেই দিতেন। বর্তমান কোন ঘটনার সঙ্গে নয়। আমরা এমন তন্ময় হয়ে যেতাম যে অনেকের পক্ষেই অশ্রু সংবরণ করা সম্ভব হত না। সত্যি বলতে কি ওঁর জন্যই বোধহয় ইতিহাস আমাকে এমন প্রচন্ডভাবে আকর্ষণ করেছিল। ইতিহাসই আমাকে সেই বয়সে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। কেন করবে না? সেই বয়সেই বুঝতে পেরেছিলাম হাবস্বুর্গের অতীত। নিজেদের স্বার্থের জন্য কিভাবে পুরো জার্মানিকে ব্যবহার করা হয়েছে। হাসবুর্গের শাসক সম্প্রদায় শুধু জার্মানদের দিয়ে নিজেদের স্বার্থই হাসিল করে নিয়েছে। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তাদের দিকে ফিরেও তাকায়নি।
হাবলুর্গের অতীতের ইতিহাস আর আজকের মধ্যে এতটুকুও ফারাক নেই। সেই একই ধারায় শোষণের পুনরাবৃত্তি ডক্টর লিওপোল্ড পোয়েটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। উত্তর ও দক্ষিণ থেকে বিদেশী রক্তের জীবগুলো, জার্মানদের নিয়ত কুরে কুরে খাচ্ছে। এমন কি ভিয়েনা পর্যন্ত অজার্মান শহর হয়ে উঠেছে। শাসক সম্প্রদায়ের প্রতিটি সুযোগ চেকদের প্রতি। বিশেষ করে এগুলোই অস্ট্রিয়ার অভ্যন্তরে চরম জার্মান জাগরণ টেনে আনে। আর্চ ডিউক ফ্রানজ ফার্দিনান্দ নিজের তৈরি গুলিতে নিজে প্রাণ হারায়। কারণ অস্ট্রিয়াকে পুরোপুরি শ্লাভদের সাম্রাজ্য করে গড়ে তুলতে তার চেষ্টার অন্ত ছিল না।
অস্ট্রিয়ার জার্মানদের এর জন্য প্রচুর রক্ত এবং অর্থ ক্ষয় করতে হয়েছিল এবং তা তারা করেছিল হাসি মুখেই। কিন্তু যখন দেখত হাসবুর্গ হিপোক্র্যাসিতে জার্মানির জার্মানরা ধরে বসে আছে যে অস্ট্রিয়া জার্মানিরই একটা প্রদেশমাত্র, তখন অস্ট্রিয়ার জার্মানরা নিরাশ না হয়ে পারেনি। অবশ্য এ নিরাশা তাদের প্রতিজ্ঞা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়নি। বরং হাবলুর্গ নামক সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্রোহী করে তুলেছিল।
কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, তখনকার জার্মান সাম্রাজ্যের শাসকেরা যেন চোখ বন্ধ করে বসেছিল। পূত গন্ধময় মৃতের পাশে দাঁড়িয়ে সেটাকেই জীবন্তরূপে কল্পনা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিল। আর দুয়ের এ বন্ধুত্বের মাঝে বিশ্বযুদ্ধের বীজাণু উপ্ত ছিল। যার পরিণতি সত্যিকারের বিশ্বযুদ্ধে।
এবার সমস্যাটার বিস্তারে আসা যাক। ছোটবেলা থেকে যে ধারণা আমার মনের ভেতরে বদ্ধমূল হয়েছিল, দিনে দিনে সেটা আরো দৃঢ়ভাবে গাঁথতে থাকে। এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি কয়েকটা ধারণায় দৃঢ় হই। প্রথমত জার্মান সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ শক্ত করতে হলে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের ধ্বংস আবশ্যক। নইলে জার্মান সাম্রাজ্যের ভিত্ ভেঙে পড়বে। দ্বিতীয়ত জাতীয়তাবাদী মানে রাজবংশীয়দের প্রতি আনুগত্য নয়। শেষে হাসবুর্গ প্রাসাদ জার্মানির ভাগ্যকাশে শনিগ্রহ বিশেষ। ইতিহাস পড়েই এ ধারণাগুলো আমার গড়ে উঠেছিল। স্কুল জীবনে ইতিহাসের প্রতি আমার যে আকর্ষণ জন্মেছিল, সেটা কোনদিনই আমাকে ছাড়েনি। আর বিশ্ব ইতিহাস হল ঘটনাগুলোর তাৎপর্য বোঝার পক্ষে খনি বিশেষ। যার জন্য রাজনীতি আমাকে আর আলাদা করে পড়তে বা লিখতে হয়নি। বিশ্ব ইতিহাসই আমার মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা এনে দিয়েছে। চলতি ভাষায় যাকে বলে অকাল পক্কো বিদ্রোহী। সাহিত্য এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে আমি ঠিক তাই ছিলাম। আপার অস্ট্রিয়ার শহরে ছোট একটা থিয়েটার হল ছিল। বারো বছর বয়সে প্রথম আমি থিয়েটার দেখতে যাই। সেটা ছিল উইলিয়াম টেল। জীবনে প্রথম দেখা থিয়েটার। কয়েক মাস পরেই দেখি আরেকটা অপেরা। লোহেনগ্রীন। জীবনে এদিকটাকে তখনো পর্যন্ত আস্বাদন করিনি। অপেরাটা দেখে এত আনন্দ পেয়েছিলাম যে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। পরবর্তী জীবনে যে শিল্পের বীজ আমার ভেতরে পরিণতি লাভ করেছিল, সেই বীজ সংগ্রহ করেছিলাম এ ছোট শহরের থিয়েটারের থেকে।
এগুলোই যেন আমাকে আমার ভবিতব্যের দিকে ঠেলে দেয় এবং বাবা তার ছেলের জন্য যে রঙিন ভবিষ্যত নিজের মনে এঁকে রেখে ছিলেন, তা থেকে আমাকে অনেক দূরে সরিয়ে দেয়। ক্রমে ক্রমে আমি যেন উপলব্ধি করতে পারি যে সঠিক পথেই আমি চলেছি। ততদিনে অর্কিটেকচার অর্থাৎ স্থাপত্য বিদ্যা বিষয়টাকে ভালবাসতে শুরু করেছি। শিল্পকর্মটা আরো বিস্তৃত পরিধি নিয়ে আমার কাছে ধরা দিয়েছে। সুতরাং অন্য কিছু হওয়ার বাসনা তখন আর আমার মনের মধ্যে নেই।
আমার যখন তেরো বছর বয়স, বাবা হঠাৎ মারা গেলেন। যদিও সেই বয়সে তার স্বাস্থ্য রীতিমত সুগঠিত, তবু রক্তের একটু উচ্চচাপ, তাতেই সব শেষ। আমরা পিতৃহারা হলেও আমার দিক থেকে একটা লাভ হল। বাবা আমাকে ছকে আঁকা ভবিষ্যতটাকে আর বেছে নিতে পীড়াপীড়ি করবেন না। তবু বাবার দৃঢ় ইচ্ছার একটা বীজ আমাদের অবচেতন মনে উপ্ত করে গিয়েছিলো।
মার মনে হল ছেলের ভবিষ্যত সম্পর্কে বাবার ইচ্ছেটাকে কার্যকরী করা তার কর্তব্য। আমার লেখাপড়ার প্রবাহটার গতিমুখ এমন দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে যাতে ভবিষ্যতে আমি সরকারি চাকরির উপযুক্ত হয়ে উঠি। কিন্তু ততদিনে আমি আরো বেশি দৃঢ় সংকল্প নিয়েছি যে কিছুতেই সরকারি কর্মচারী হব না। কিন্তু স্কুলের শিক্ষাদীক্ষা তো একই খাতে প্রবাহিত। ছাত্রদের সরকারি চাকরির উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। কিন্তু অসুখ এসে যেন বাঁচিয়ে দিল। ডাক্তার আমার ফুসফুসের অবস্থা দেখে মাকে জানাল যে আমার ফুসফুসের যা অবস্থা তাতে ভবিষ্যতে চার দেওয়ালের বদ্ধ আবহাওয়ায় চাকরি করা উচিত নয়। বরং বছর খানেকের জন্য স্কুল থেকে ছুটি নেওয়া দরকার। নইলে শরীর সেরে ওঠার কোন সম্ভাবনা নেই। আঃ, আমি যেন বেঁচে গেলাম। এতদিন ধরে মনেপ্রাণে যা চাইছিলাম তা বাস্তবে মূর্ত হয়ে ধরা দিল। হ্যাঁ, অকল্পনীয়ভাবে। ডাক্তারের কথাবার্তা শুনে মা রাজী হল। আমি স্কুল ছেড়ে দিয়ে আকাদেমিতে ভর্তি হলাম।
কিন্তু সেই সুখের দিনগুলো যেন একটা স্বপ্ন। দেখা দিয়েই বুদ্বুদের মত মিলিয়ে গেল। বছর দুই বাদে মার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনের রঙিন স্বপ্ন সৌধগুলো তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ল। দীর্ঘদিন মা ভুগছিলেন। যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠতেন। তখনই বুঝেছিলাম মা আর বেশি দিন বাঁচবেন না। যদিও মার মৃত্যু খুব একটা অকস্মাৎ নয়, তবু জীবনে প্রচন্ড একটা ধাক্কা খেলাম। বাবাকে শ্রদ্ধা করতাম, কিন্তু মা’কে ভালবাসতাম।
দারিদ্রতা আর নিষ্ঠুর বাস্তব করালরূপ ধরে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। সংসারে সঞ্চয় বলতে যা ছিল মার দীর্ঘ রোগভোগের সময়েই তা নিঃশেষ। অনাথ হিসেবে সরকারি তহবিল থেকে যা পেতাম তা আমার বেঁচে থাকার পক্ষে যথেষ্ট নয়। সুতরাং রুটির তাগাদা অনুভব করলাম।
একটা ছোট চামড়ার সুটকেশে জামাকাপড় আর মনের ভেতরে অদম্য ইচ্ছেটাকে পুরে নিয়ে আমি ভিয়েনার রাস্তা ধরি। অজানা ভবিষ্যত; যেমন আমার বাবা প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ভাগ্যকে ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দিয়ে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তবু মনে দৃঢ়তা ছিল। জীবনে কিছু করবই— কিন্তু সরকারি চাকুরে হব না।
০২. ভিয়েনার যন্ত্রণাময় বছরগুলো
মা’র মৃত্যুর পর আমার ভাগ্য নৌকোর হাল একমুখী। মা’র অসুখের শেষের দিকে একবার ভিয়েনায় গিয়েছিলাম আকাদমি অফ্ ফাইন আর্টসে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। পকেটে এক গাদা স্কেচ নিয়ে আমি তখন নিশ্চিত যে অতি সহজেই পরীক্ষাটায় উরোবো। স্কুলে ড্রইয়ে বরাবর ভাল রেজাল্ট করেছি। ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছি। সুতরাং ড্রইংয়ে আমার ক্ষমতা প্রশ্নাতীত। তাই বুক ভরা গর্ব ছিল যে সেই দক্ষতার জোরে প্রবেশ পরীক্ষার সমুদ্র পার হওয়া আমার পক্ষে কিছুই নয়।
কিন্তু আমার ভুল ঠিক কোথায় আকাদমিতে পরীক্ষা দিতে এসে বুঝতে পারি। ড্রইংয়ে আমার হাত পাকা হলেও অঙ্কন শিল্পে নয়। বিশেষ করে আর্কিটেক্টারাল অর্থাৎ স্থাপত্য বিদ্যার ড্রইংয়ে। তখন স্থাপত্য বিদ্যায় আমার উৎসাহ বাড়ছে। এবং ভিয়েনায় দু’সপ্তাহ কাটিয়ে আসার পরে স্থাপত্য বিদ্যার তৃষ্ণা আরো বেশি তীব্র হয়ে ওঠে। তখনো আমার বয়স সোল পূর্ণ হয়নি। হোফ মিউজিয়ামে যাতায়াত শুরু করি, আর্ট গ্যালারির ছবিগুলো খুঁটিয়ে দেখার জন্য। কিন্তু ছবির বদলে হোফ মিউজিয়ামের বাড়িটার গঠনশৈলী আমাকে অনেক বেশি আকর্ষণ করে। সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত রাস্তায় ঘুরে ঘুরে প্রাচীন বাড়িগুলোর গঠন নৈপুণ্য লক্ষ্য করতাম। এবং প্রায় ভেঙে পড়া অতি পুরনো বাড়িগুলো কি এক অদ্ভুত আকর্ষণে আমাকে টানতো। কিছুতেই স্থির থাকতে দিত না। ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দিতাম অপেরা হাউস বা পার্লামেন্টের সামনে। বিশেষ করে পুরো রি স্ট্রীটটা আমাকে যেন ভানুমতীর যাদু করেছিল। মনে হত বাড়িঘরগুলো আরব্য রজনীর পাতা থেকে হঠাৎ উঠে আসা কোন দৃশ্যপট।
এবার নিয়ে দ্বিতীয়বার আমি এ সুন্দরী নগরী ভিয়েনায় আসি; অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকি প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলাফলের জন্য। অবশ্য নিজের মনে নিশ্চিত যে এ পরীক্ষায় পাশ আমি করবই। কিন্তু বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত ফলাফল বেরোলে দেখি পাশ করতে পারিনি। বিশ্বাস করা কঠিন। তবু সত্যি আমি যে আমি পাশ করিনি। সুতরাং অধ্যক্ষর সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করি যে কেন আমি আকাদমীর অংকন বিভাগে সুযোগ পাব না। অধ্যক্ষ জানালেন, যে স্কেচগুলো আমি পরীক্ষার ব্যাপারে দাখিল করেছি সেগুলো থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে আর্কিটেকচারে আমার দখল অনেক বেশি, অংকন শিল্পের চেয়ে। সুতরাং অংকন শিল্প বিভাগে আমাকে নেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। তবে আকাদমির আরেক বিভাগ আর্কিটেকচারে নেওয়া যেতে পারে। মানে? আমার বিস্ময় তখন তুঙ্গে। স্থাপত্যবিদ্যা সম্পর্কে আমার বিশেষ কোন জ্ঞানই নেই। এমন কি কারোর থেকে আর্কিটেকচার ড্রইং সম্পর্কে কোন শিক্ষাও পাইনি।
শিলার প্লাটৎজের হানসেন প্যালস ছেড়ে যখন বেরিয়ে আসি, তখন আমি নিরাশার গভীর সমুদ্রে নিমজ্জিত। এ বয়সে প্রথম যেন জীবনে নিজেকে ছোট বলে মনে হয়। যার জন্য নিজেকে উপযুক্ত বলে এতদিন ভেবে এসেছি, স্বপ্নের সেই সৌধ আজ মুহূর্তে ভেঙে পড়ে।
কয়েকদিনের মধ্যে মনের জোর আবার খুঁজে পাই। আর্কিটেকটু আমাকে হতেই হবে। যদিও জানি সে পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়; বরং অনেক কঠিন। আকাদমির আর্কিটেকচার বিভাগে যোগদানের আগে আমাকে টেকনিক্যাল বিল্ডিং স্কুলে পড়তে হবে। কিন্তু স্কুলে পড়ার অধিকার পেতে হলে মাধ্যমিক স্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাশের সার্টিফিকেট চাই, যেটা আমার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়, আমার স্বপ্ন আমার ক্ষমতাকে ছাড়িয়ে।
মার মৃত্যুর পর তৃতীয় বার ভিয়েনায় আসি। অবশ্য এবারে বেশ কয়েক বছরের জন্য। এতদিনে আবার আত্মবিশ্বাসটা ফিরে এসেছে। সুতরাং লক্ষ্যের দিকে আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ। আমাকে আর্কিটেক্ট হতেই হবে। জীবনের পথে বাধা তো থাকবেই। যে করেই হোক সেগুলো ডিঙিয়ে যাব। তাছাড়া বাবার স্মৃতি তো চোখের সামনে সব সময় ভাসছে। দরিদ্র চর্মকারের সন্তান হয়েও কত সংগ্রাম করে তাঁকে সরকারি চাকুরে হতে হয়েছে। তার চেয়ে আমার জীবনের শুরু তো অনেক মসৃণ, আমার যুদ্ধের প্রতিকূলতাও বাবার পরিবেশের মত তীক্ষ্ণ নয়। তখন অবশ্য মনের দিক থেকে এমন একটা অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছি যে বারবার মনে হয় ভাগ্যদেবী নিদারুণ হাতে কষাঘাত করে চলেছে। আমার প্রতি বিমুখ, নির্দয়। তবু ইচ্ছা বেগবতী নদী; বাধা পেলে আরো ফুলে ফেঁপে ওঠে। শেষ পর্যন্ত আমার সেই অদম্য ইচ্ছাশক্তিটাই জয়ী হয়।
জীবনের এ অধ্যবসায়টার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। কারণ জীবনের এ পর্বটাই আমাকে শক্ত আর অনমনীয় করে তুলেছিল। সেই কারণে খুব কাছে থেকে জীবনটাকে চিনতে পেরেছি। সত্যি বলতে কি আজকে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে, এখানে আমার পক্ষে ওঠা সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র জীবনের এ অধ্যায়টার জন্য। এবং জীবনের এ দিনগুলোই আমাকে শূন্যতার হাত থেকে বাঁচিয়েছে। স্নিগ্ধ মায়ের কোল থেকে ছুঁড়ে দিয়েছে রুক্ষ আরেক নতুন মায়ের হাতে। যদিও এ দুঃসময়ে চরম দারিদ্রতার মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার জন্য নিষ্ঠুর ভাগ্যের প্রতি মাঝে মাঝে মনটা বিদ্রোহ করে উঠেছে; তবু যাদের জন্য পরবর্তী জীবনে আমি সংগ্রাম করেছি, এ পথেই আমি সেসব মানুষদের কাছে এসে দাঁড়াতে পেরেছি।
এ সময়ে আমি জাতির অস্তিত্বের পক্ষে দুটো বিপদ উপলব্ধি করতে পারি। একটা মার্কসইজম্ আরেকটা হল জুডোইজম বা ইহুদী ধর্মমত।
অনেকের কাছেই ভিয়েনা তখন প্রমোদ নগরী। আনন্দের মুহূর্তগুলো উপভোগের নিমিত্ত বেহিসেবী খরচের জায়গা। কিন্তু আমার কাছে। সে বছরগুলো শুধু দুঃস্বপ্ন বিশেষ। এমন কি সেই দিনগুলোর কথা ভাবলে আজকে পর্যন্ত মনটা বিষাদে ভরে ওঠে। সেই স্মৃতিচিহ্নগুলোর একটাতেও যদি এতটুকু রঙের ছোঁয়া থাকত। সুদীর্ঘ পাঁচ বছরের প্রতিটি দিন রাহুগ্রস্ত যেন প্যাসিয়ান শহরের দিনগুলো। হোমারের ওডিসি কাব্যের রূপক হল প্যাসিয়ান লোকগুলো, তারা ভূমধ্যসাগরের পূর্বদিকের কোন এক অজানা দ্বীপে বসবাস করত। কেউ কেউ বলে আজকে সেই দ্বীপের নামকরণ হয়েছে কোরসিয়া, আধুনিক সুসজ্জিত কর্য। তারা কাজের চেয়ে জীবনটাকে উপভোগ করতে বেশি ভালবাসত। তাই ওডিসি কাব্যে তাদের নামকরণ করা হয়েছে প্যাসিয়ান। যার অর্থ ক্রমে ক্রমে দাঁড়িয়েছে প্যারাসাইট বা সমাজের পরগাছা।
এ পাঁচ বছরে কখনো দৈনিক শ্রমিক অথবা তুচ্ছ ছবি এঁকে আমাকে রুটির জোগাড় করতে হয়েছে। তবু পেট ভরাতে পারিনি। সব সময়ই ক্ষুধা আমার পিছু পিছু তাড়া করে ফিরেছে। সেই সময় একটা বই কেনা বা একবার অপেরায় যাওয়ার মানে হল পরের কয়েকটা দিন মুখিয়ে থাকা ক্ষুধায় ফু দিয়ে আগুন জ্বালানো। তবু এদিনগুলোতেই শিখেছি আমি সবচেয়ে বেশি। আর্কিটেকচারাল স্টাডি অর্থাৎ স্থাপত্যবিদ্যার পড়াশোনার বাইরে মাঝে মাঝে কশ্চিৎ কখনো অপেরায় যেতাম। তখনকার জীবনে বিলাসিতা বলতে ঠিক এটুকুই। আর বই। হ্যাঁ, বই-ই ছিল ক্ষুধা ছাড়া আমার নিত্যসঙ্গী।
তখন আমি খুব পড়তাম। এবং যা যা পড়তাম সেই বিষয়গুলোকে চেষ্টা করতাম মনপ্রাণ দিয়ে অনুভব করতে। যেটুকু সময় ফাঁকা পেতাম পড়াশোনার মধ্যে ডুবে থাকতাম। সেই অল্প কয়েকটা বছরে বই পড়ে যে জ্ঞান আমি অর্জন করেছিলাম, বলতে দ্বিধা নেই আজও তা কাজে লাগছে। তার চেয়েও বড় কথা জীবন সম্পর্কে স্বচ্ছ একটা দৃষ্টিভঙ্গি আর পৃথিবী সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা আমার সে সময়েই গড়ে ওঠে। যেটা ভবিষ্যত জীবনে আজ পর্যন্ত বদলায়নি। উপরন্তু আমার দৃঢ় ধারণা, যৌবনের বছরগুলো মানুষকে যে অভিজ্ঞতার বনিয়াদ গড়ে দেয়, ভবিষ্যতের জ্ঞানের প্রাসাদ তাকেই ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। যৌবনের ধ্যান ধারণাগুলোই ভবিষ্যতের রঙিন ফুল। যদি অবশ্য তার মধ্যে সৃষ্টির বীজ বোনা থাকে। যৌবনের সৃষ্টির চিন্তাধারা ভবিষ্যতের প্রাসাদ নির্মাণের রসদ।
আমার বাল্যকাল যাদের সঙ্গে কেটেছে, তাদের জীবনধারার সঙ্গে আমার জীবনের কোন পার্থক্য ছিল না। আমার ছোটবেলা কেটেছে নিচুস্তরের বুর্জুয়া অর্থাৎ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে। সুতরাং সত্যিকারের মেহনতী মানুষদের সঙ্গে আমার পরিচিত তখন হয়নি। সম্ভবও ছিল না। যে অর্থনৈতিক পরিখাটা এ দুই শ্রেণীর মাঝখানে ছিল সেটা মোটেই গভীর নয়। বরং অনেক সময় মেহনতি শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থা ভাল ছিল। তবে কেন এ পার্থক্য? আসলে মেহনতী জনগণের একটা দল যারা একটু উঁচুতে উঠেছিল, তারা চাইত মেহনতী জনগণের ওপর মাতব্বরী করতে অথবা যেখান থেকে তারা উঠেছে, টালমাটাল হয়ে আবার সেখানেই পড়ে যেতে পারে এ ভয়ে তারা মেহনতী জনগণের থেকে দূরে সরে থাকত। আসলে পুরনো দিনের যে রুক্ষ স্মৃতিটা পেরিয়ে এসে তারা সিঁড়ির সবচেয়ে নিচেকার ধাপটা ধরেছে, সেখান থেকে গড়িয়ে পড়ে যাওয়ার ভয়টাই তাদের সব সময় শঙ্কিত করে রাখত। যে জীবন অতিকষ্টে পেরিয়ে এসেছে সেখানে গিয়ে কিছুতেই আর দাঁড়াতে চাইত না।
এ কারণেই সম্ভবত সত্যিকারের যারা সমাজের ওপরতলার বাসিন্দা, তারা যতটা চট করে সমাজের একবারে নিচুস্তরের সঙ্গে মিশতে পারত, হঠাৎ এ ভূঁইফোড়দের পক্ষে সেটা কিছুতেই সম্ভব ছিল না। হয়তো বা যে প্রচণ্ড সংগ্রাম করে এসব উঁইফোড়দের দল নিচের তলার বাসিন্দাদের ছাড়িয়ে উপরে উঠেছে, সেই নিদারুণ সংগ্রামের জন্য মানুষের মনের সুকোমল প্রবৃত্তিগুলোই মরে গেছে। নতুবা জীবনযুদ্ধে যুঝতে গিয়ে অপরের দিকে তাকাবার আর ফুরসৎ পায়নি।
এদিক থেকে ভাগ্য আমার ভাল ছিল বলতে হবে। অবস্থা বিপর্যয়ে আমার ছেলেবেলাকার ভূঁইফোড়দের যে জগতে বাস, নিদারুণ দারিদ্রতা আর অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেদিনকার বুর্জুয়া জীবনের রঙিন ছবিটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়েছিল। জীবনে এ প্রথম আমি হামবাড়া আর সত্যিকারের ভাল লোকদের মধ্যে ফারাক বুঝতে শিখি। মানুষকে চিনি অনেক কাছে থেকে। যাদের রঙ অভিজ্ঞতা থাকলে ধরা অসম্ভব।
বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধে পৃথিবীর যে ক’টা শহর অপরাধীতে অধ্যুষিত ছিল, ভিয়েনা তন্মধ্যে অন্যতম। হঠাৎ ফুলে ফেঁপে ওঠা প্রাচুর্যের পাশে চরমতম দারিদ্রতা পাশাপাশি বিরাজমান। বাহান্ন মিলিয়ান বিভিন্ন জাতির লোকসংখ্যা সমৃদ্ধ এ শহরের ভেতরে ঢুকলেই এটা স্পষ্ট বোঝা যেত। প্রাসাদগুলো উপচে পড়া ঐশ্বর্যের প্রতীক। বিশেষ করে সাধারণকে বঞ্চিত করে এ ঐশ্বর্যের স্থূপ প্রাসাদে প্রাসাদে সবচেয়ে বেশি জমা হয় হাববুর্গ শাসনকালে।
এ কেন্দ্রে সবকিছু জমা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল সম্ভবত পাঁচমিশেলী জনসাধারণের জন্য। সুতরাং শহরের কেন্দ্রে উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং রাজার বসবাস গড়ে ওঠে।
কিন্তু দানুবিয়ান শাসকের সময় ভিয়েনা শুধু রাজনৈতিক এবং সংস্কৃতির পীঠস্থান ছিল না। বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবেও শহরটা গড়ে উঠেছিল। তাই সামরিক, অসামরিক অফিসার, বিজ্ঞানী এবং শিল্পী ছাড়া প্রচুর শ্রমিক শহরের অভ্যন্তরে বসবাস করত। দারিদ্রতার সঙ্গে এ অভিজাত ধনী ব্যবসায়িক সম্প্রদায়ের প্রায়ই মুখোমুখি সংঘর্ষ নেগে থাকত। হাজার হাজার বেকার উদ্দেশ্যহীনভাবে রিঙ স্ট্রীটের প্রাসাদগুলোর সামনে ঘুরে বেড়াত; এবং পুরনো অস্ট্রিয়ার ভায়া ট্রায়াম্ফ ফালিসের নিচে নরক গুলজার করত। অবশ্য তখনকার প্রায় প্রতিটি জার্মান শহরই এরকম ছিল। এ সমস্যাটা আলোচনা করার আগে যথেষ্ট সতর্কতা প্রয়োজন। প্রথমত ওপরতলা থেকে এ সমস্যাটা সম্পূর্ণরূপে বোঝা সম্ভব নয়, এ বিষাক্ত ভাইপারের কবলে যে না পড়েছে, তার পক্ষে বোঝা অসম্ভব যে এর বিষ কত তীব্র হতে পারে। নিজে ভুক্তভোগী না হলে এ সমস্যাটা শুধু আলোচনার স্তরেই থেকে যেতে বাধ্য। এর শিকড়ে পৌঁছানো আদৌ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত এটাকে এড়িয়ে যাওয়ার আরেকটা পথ সমস্যাটার দিকে পেছন ফিরে থাকা, অথবা মৌখিক সহানুভূতি দেখানো। কিন্তু তাতে ক্ষতি বৈ লাভ হয় না। তখন অবশ্য এরাই আবার তাদের অকৃতজ্ঞ বলে গালাগাল করে।
ধীরে ধীরে মানুষগুলো এক সময় বুঝতে পারে যে এ সামাজিক পরিবেশে সমাজ সংস্কারের কাজ করে কোন লাভ নেই। কারণ পুরো সমাজটার গঠনই এমন যে কৃতজ্ঞতা বলে জিনিসটাই সমাজের বুক থেকে অন্তর্হিত। সুতরাং সমাজের কাছ থেকে বিনিময়ে কিছু পাওয়ার আশা দুরাশা মাত্র; বরং প্রাপ্য যদি কিছু হয় তা হল অন্যায় বিচার। সামাজিক সমস্যাগুলো সম্পর্কে জানবার লোভ থাকলেও সেই সময়ের আমার দারিদ্র পীড়িত অবস্থাই আমাকে সেদিকে পা বাড়াতে দেয়নি। অবশ্য এভাবে কোন সমস্যাই দূর থেকে বোঝা সম্ভব নয়, যদি না কেউ তাতে জড়িয়ে পড়ে। তাই বলা যেতে পারে যে, শশক যদিও গবেষণাগারের পাশ কাটিয়ে এসেছে, তবু একেবারে তার ক্ষতি হয়নি তা বলা যায় না।
যখন আমি আজ সেইদিনগুলোকে স্মরণে আনতে চেষ্টা করি, পুরোটা কিছুতেই পারি না। তাই এখানে আমি সেই ঘটনাগুলোর কথাই বলব যেগুলো আমায় ব্যক্তিগতভাবে আঘাত করে বদ্ধ এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। যার থেকে অনেক ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আমি লাভ করেছি।
সেই দিনগুলোতে আমার পক্ষে চাকরি জোগাড় করা কষ্টকর হলেও একেবারে অসম্ভব ছিল না। তার প্রধান কারণ হল আমি কুশলী শ্রমিক দলে পড়তাম না। কুলি কামারের কাজ যেগুলো অন্য কেউ করতে চাইত না, আমি পেটের দায়ে সেগুলোই জুটিয়ে নিতাম।
অন্যান্য যারা নিজেদের দেশ ছেড়ে প্রবাসী হয়ে পা থেকে ইউরোপের ধুলো ঝেড়ে লৌহকঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়ে এ নতুন দেশে নতুন জগতে নতুন নীড় তৈরি করতে আসে, আমিও সেই দলেরই একটি নতুন মুখ। শ্রেণী সংস্কার ইত্যাদি সমস্ত কিছু পেছনে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য তারা চাকরিক্ষেত্রে যে দরজা খোলা পায় তা দিয়েই ঢুকে পড়ে। আসলে এখানে এসে তারা উপলব্ধী করতে পারে শ্রমের মর্যাদা। কোন কাজই কাউকে ছোট করে না, যদি তা সততার সঙ্গে সম্পন্ন করা যায়। আর এ চিন্তাধারাই আমাকে নতুন জগতের নতুন রাস্তায় এগিয়ে যাবার প্রেরণা দিয়েছিল।
অতি শীঘ্র বুঝতে পারলাম এ ধরনের কাজ যেমন সব সময় জোগাড় করা যায়, তেমনি চট করে চোখের পলকে সেই চাকরি চলেও যায়।
দৈনিক রুটি জোগাড়ের এ অনিশ্চয়তাই আমার এ নতুন জগতের দিনগুলোকে বিন্ন করে তুলেছিল।
যদিও শিক্ষিত শ্রমিকদের কুলি কামারদের মত যখন তখন চাকরি থেকে বরখাস্ত করে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হত না, তবু তাদের চাকরির নিশ্চয়তা বলে তেমন কিছু ছিল না। তাই শিক্ষিত শ্রমিক দলের একেবারে অনাহারের মুখোমুখি হতে না হলেও বেকারী, ধর্মঘট আর লক্ আউটের দরুন প্রতিদিনই তাদের রুটির চিন্তায় বিপর্যস্ত থাকতে হত। এ দৈনন্দিন রুটির অনিশ্চয়তা সামাজিক অর্থনীতির অন্ধকারময় দিক।
গ্রামে থেকে অনেক ছেলে শহরে সহজ কাজের লোভে চলে আসে। সহজ কাজ মানে কয়েক ঘন্টার কাজ। অবশ্য সেই সঙ্গে শহর জীবনের রহস্যময়তাও তাদের আকর্ষণ করত। গ্রামে তবু যা হোক বাঁধাধরা একটা রোজগার ছিল। কারণ চাষাবাসের কাজে লোক খুঁজে পাওয়া তখন রীতিমত কষ্টকর। অনেকেই শহরের সহজ জীবনযাত্রার হাতছানিতে গ্রাম ছেড়ে শহরের দিকে পাড়ী দিয়েছে। তবু যারা গ্রাম ছেড়ে দিয়ে শহরে আসত তাদের অবস্থা গ্রামে থাকা লোকদের থেকে খারাপ ছিল একথা বলা যায় না। অবশ্য আমি প্রবাসী বলতে যারা আমেরিকায় পাড়ী দিয়েছে তাদের কথা বলছি না। যারা গ্রাম ছেড়ে শহরে আসত তাদেরও আমি প্রবাসী বলেই মনে করি। কারণ সরল যে ছেলেটা বেশি রোজগারের আশায় গ্রাম ছেড়ে শহরে আসে, শহর জীবনে সে তো সম্পূর্ণ বিদেশী। অবশ্য অনিশ্চিত জীবনের ঝুঁকি নিয়েই সে শহরে এসেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পকেটে গোনাগুণতি পয়সা নিয়ে আসা ছেলেগুলোর ভাগ্য খুব খারাপ না থাকলে প্রথম কিছুদিন মন্দ কাটত না। কিন্তু চাকরি পেয়ে অল্পদিনের মধ্যে হারালেই, যা অহরহ ঘটত, অবস্থা তাদের শোচনীয় হয়ে উঠত। বিশেষ করে শীতের সময় তো অসম্ভব। অবশ্য চাকরি যাওয়ার পরের কয়েকটা সপ্তাহ ততবেশি দুঃসহ ছিল না। পকেটে তখন শেষ মাইনের রেস্ত কিছুটা অবশিষ্ট। ট্রেড ইউনিয়ন থেকে তখন পর্যন্ত পাওয়া বেকার ভাতার টাকায় দিনগুলো চলে যেত। কিন্তু একসময়ে শেষ মাইনের টাকাটা আর দীর্ঘ বেকারত্বের জন্য ট্রেড ইউনিয়নের বেকার ভাতাও বন্ধ হয়ে যেত। তখনই পড়তে হত অসহনীয় দুর্দশার মধ্যে। পেটের জ্বালায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো ছাড়া উপায় কি? উপায় বলতে অবশিষ্ট যা কিছু তা বন্ধক দেওয়া বা বিক্রি করা। কিন্তু সে পয়সায় আর কতদিন চলে। জামাকাপড় ততদিনে নোংরা আর শতচ্ছিন্ন। বাইরের অবয়বেও দারিদ্রতার ছাপ ফুটে উঠেছে। বাধ্য হয়ে সমাজের নিম্নস্তরের লোকগুলোর সঙ্গে মেলামেশা করতে হত, যাদের চিন্তাধারায় মন যায় বিষিয়ে। তদুপরি শারীরিক দুর্দশা তো আছেই। উপরন্তু মাথা গোঁজার ঠাঁই কোথায় পাবে? শীতের দিন হলে তো দুর্দশার একশেষ। শেষমেষ যদি আবার প্রাণপণ চেষ্টাতে একটা চাকরি যোগাড় করতে পারে; কিন্তু সেটা তো আবার আগেকার ব্যাপারটাই পুনরাবৃত্তি। তৃতীয় বারেও সেই একই নাটক। অর্থাৎ দিনে দিনে সে আরও বেশি হতাশা আর অনিশ্চয়তার সমুদ্রে নিমজ্জমান। ধীরে ধীরে পুরো ব্যাপারটাই তার কাছে একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে কঠোর পরিশ্রমে একটা লোক তার জীবনের প্রতি উদাসীন আর অমনযোগী হয়ে ওঠে। এবং একসময় কতগুলো ঠগ জোচ্চরের হাতের পুতুল হয়ে পড়ে, যারা তাদের নিজেদের অসৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাকে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহার করে। এত বেশি বেকারত্বের বোঝা বইতে স্ট্রাইক, দেশের অর্থনৈতিক ক্ষতি, নিজের ভবিষ্যত অনিশ্চিয়তার ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে পুরোপুরি উদাসীন হয়ে পড়ে। যদিও সে মনেপ্রাণে স্ট্রাইক ইত্যাদি ব্যাপারগুলো চায় না; তবু মনের সব অনুভূতি হারিয়ে ফেলে সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে ধর্মঘটীদের দলে ভিড়ে যায়।
এরকম বহু উদাহরণ আমি দিনের পর দিন দেখিছি। যতদিন গেছে, এ দানব শহরটা যেভাবে পাগলের মত লোকগুলোকে আকর্ষণ করে তা দেখে দেখে শহরটার প্রতি মনের মধ্যে একটা তিক্ততা জন্মে গেছে। প্রথম যখন তারা গ্রাম ছেড়ে শহরে আসে, কিছুদিন পর্যন্ত সেই গ্রাম্য জীবনের সংগে তাদের একটা যোগাযোগ বজায় থাকে, তারপর, একদিন তাদের অলেক্ষ্যে ছিঁড়ে যায়।
আমি সেই শহর জীবনের আবর্তে পড়ে বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার ভাগ্যও সেই লোকগুলোর মত; এবং আমার ওপরেও শহুরে জীবন তার থাবা নিয়ত বসিয়ে চলেছে। এ অর্থনৈতিক ওঠা নামায় স্বভাবতই তার খরচা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। যখন পকেটে পয়সা থাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খায়; বাকি সময় অনাহারে কাটায়। এটা শারীরিক একটা চক্রের আবর্ত। ক্ষুধার্ত অবস্থায় দীর্ঘদিন কাটানোর সময় যে স্বপ্ন দেখে খাওয়ার দিনগুলোর। এবং এ স্বপ্নগুলো তার মানসিক অবস্থাকে এমন এক জায়গায় পৌঁছে দেয় যে সে এ খরচা নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মানসিক ভারসাম্য একেবারে হারিয়ে ফেলে। তাই আবার যখন সে চাকরি পায়, মাইনের দিনগুলোর আগামীদিনের কথা মনে না রেখে পুরোটাই খরচা করে বসে। এটা যে শুধু তার ব্যক্তিগত জীবনের অভাব ডেকে আনে তা নয়, তার এ স্বল্প সাপ্তাহিক বেতনে গৃহের প্রয়োজনীয় খরচের হিসেবও রাখতে পারে না। ব্যাপারটা এরকম; প্রথম দিকে তার সাপ্তাহিক রোজগারে পাঁচদিন কোন রকমে চলে যায়; তারপরে অভ্যাসটা বাড়তে বাড়তে সেই একই রোজগারে তিনদিন পার হওয়া মুস্কিল হয়ে পড়ে। শেষে সেটা গিয়ে দাঁড়ায় একদিনে। অবশেষে এক উৎসবের রাত্রেই পুরো সাপ্তাহিক মাইনে সে খুঁকে দেয়। এগুলোর একমাত্র কারণ হল তার নিজস্ব রোজগারে খরচা করার বাজেট তৈরি করার অক্ষমতা।
অনেক সময়েই তাদের ঘরে স্ত্রী পুত্র থাকে। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার এ অভ্যাস ওদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়; বিশেষ করে স্বামী যদি তার পরিবারকে নিজস্ব ধরনে ভালবাসে আর সেই পরিবারকে জড়িয়ে ধরে দিনগুলোকে পাড়ী দিতে চায়; সেই ক্ষেত্রে পুরো সপ্তাহের রোজগারে পরিবারটির তিন চার দিনের ভরণপোষণ কোনক্রমে চলে। যতদিন টাকা থাকে সবাই মিলে খাদ্য আর পানীয়ের মহাফিল জুড়ে দেয়, সপ্তাহের বাকি দিনগুলো তারপর ওদের কাটে অনাহারে। তখন তার স্ত্রী প্রতিবেশীদের থেকে গোপনে ধার করে আর পাড়ার দোকানদারদের কাছে সামান্য জিনিসের জন্য হাত পেতে দুঃখের দিনগুলো পাড়ি দিতে চায়। পুরো পরিবারটা শূন্য খাবার টেবিলে বসে মনে মনে কল্পনা করে আগামী সপ্তাহে এ অভাবের আর যেন পুনরাবৃত্তি না হয়। আর সেই ক্ষুধার দিনগুলোয় স্বপ্ন দেখে প্রাচুর্যের দিনে পেট ভরে খাওয়ার। এবং শিশুকাল থেকেই এ দুঃখের দিনগুলোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওরা এ জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।
এ অভাবরূপী শয়তান পুরুষটাকে সপ্তাহের প্রথম দিকে তাড়া করে ফেরে। স্ত্রী স্বভাবতই ছেলে মেয়েদের মুখ চেয়ে সংসারের দাবি আদায়ের জন্য সচেষ্ট হয়। ক্রমে সেটা রূপ নেয় কদর্য কুৎসিত ঝগড়ায়। স্বামী আর কোন পথ খুঁজে না পেয়ে মদ খেতে আরম্ভ করে। দিনে দিনে পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে মনের দিক থেকে অনেক দূরে সরে যায়। তারপর মানুষটার শুরু হয় প্রতি শনিবারে মদ খাওয়া; স্ত্রী তার এবং সন্তানদের অস্তিত্ব রাখার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রামে নামতে বাধ্য হয়। কারখানার রাস্তা থেকে নোংরা পুঁড়িখানা পর্যন্ত কয়েকটা পয়সার জন্য মাইনের দিনে স্বামীকে ধাওয়া করে। সব পয়সা খুইয়ে রোববার বা সোমবার যখন সে বাড়ি ফেরে তখন সম্পূর্ণ নিঃস্ব। আবার অভাব অনটন, ঝগড়াঝাটি, শেষে ভগবানের দাহাই পেড়ে চিৎকার আর কান্নাকাটিতে ভরা প্রহরগুলো কাটে।
এরকম শয়ে শয়ে ঘটনা আমার চোখের ওপর দেখেছি। প্রথমে বিরক্ত হলেও পরে পুরো ব্যাপারটার মধ্যে ট্রাজেডি এবং দুর্ভাগ্য কোথায় বুঝতে অসুবিধে হয়নি। ওরা হল শয়তান সমাজ ব্যবস্থার শিকারমাত্র।
তখনকার পারিবারিক অবস্থা প্রায় সব পরিবারেই এক। বিশেষ করে ভিয়েনার শ্রমিকেরা চারিদিকে দুঃখ-দুর্দশার দেওয়ালের মধ্যে দিন যাপন করত। এখনো যখন সেই দুঃখের দিনগুলো আমার স্মৃতির সামনে ভেসে ওঠে, সারা শরীরটা ভয়ে কাঁপতে থাকে। গভীর নিঝুম রাত্রে বস্তি থেকে ভেসে আসা মাতাল স্বামীর সঙ্গে তার স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের ঝগড়া আর নিষ্ঠুর মারামারি। ক্লেদাক্ত পরিবেশে ওদের জীবনযাত্রা মানুষকে এক একটা পুরো শয়তান বানিয়ে ছাড়ে।
সেদিন কি হবে যেদিন মানুষগুলো নিজেদের অবস্থা বুঝতে পেরে যারা তাদের এ অবস্থায় এনে ফেলেছে তাদের তাড়া করবে? কিন্তু আশ্চর্যের কথা সে জগতের বাসিন্দারা এ জগতের লোকদের কোন খোঁজ খবরই রাখে না। কিন্তু একদিন আসবে যখন পুরো ঘটনাটা তার আপন গতিপথে মোড় নেবে, যদি না সময় মত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।
আজ এতদিন পরে আমি আমার ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানাই এজন্য যে নিয়তি আমাকে এমন একটা বিদ্যালয়ে ঘটনাক্রমে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল, ইচ্ছে না থাকলেও সেই পরিবেশে বাধ্য হয়েছি ঘটনাগুলোর প্রতি মন সংযোগ করতে। এ স্কুলই আমাকে জীবনের এক শক্ত বুনিয়াদের ওপর এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।
পুরোপুরি নিজেকে হতাশার সমুদ্রে নিমজ্জিত না করার জন্য আমি তঙ্কালীন পরিবেশটাকে দু’ভাগে ভাগ করি। এক, বাইরের চেহারা অনুযায়ী; দুই যে যে কারণে তারা এরকম পরিবেশে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছে। এ একমাত্র পথ যার দ্বারা নিজেকে হতাশা সমুদ্রে পুরোপুরি ডোবার হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছি। তারা এ দুঃখ দুর্দশায় এবং দুর্ভাগ্যের সমুদ্রে ডুবে নিজেদের এ নোংরা পরিবেশ এবং নিচুতে নামাতে বাধ্য হয়েছে। তাদের অবস্থা সত্যই শোচনীয়। আমার জীবনেও এ একই ধরনের দুর্দশা আমাকে মানুষগুলোর প্রতি ভাবালু হতে দেয়নি। না, ভাবালু হয়ে পড়লে কোন কিছুরই সঠিক মূল্যায়ণ সম্ভব নয়।
সে দিনগুলোতে আমি বুঝতে পারতাম যে একমাত্র এ অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য দুটো পথ খোলা আছে। এক সামাজিক অবস্থার পুরো একটা পরিবর্তন এনে নিচেকার লোকদের সমাজের প্রতি কর্তব্য এবং দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। দুই, এ কর্তব্য এবং দায়িত্ব বোধের সমন্বয় সাধন করে নিষ্ঠুর হাতে সমাজের অপ্রয়োজনীয় অনুশাসন তথা শুকনো ডালপালা হেঁটে দিতে হবে— যেগুলো এ সমাজটাকে সুস্থভাবে বাড়তে দিচ্ছে না।
প্রকৃতি যেমন স্থিতাবস্থায় থাকে না, তেমনি মানুষের জীবনেও যান্ত্রিক উপায়ে উন্নতি সাধন করা অসম্ভব। জন্মের পর থেকেই তার ভবিষ্যতের উন্নতির জন্য একটা সুনির্দিষ্ট এবং পাকা রাস্তা চাই, যেটা ধরে সে তরতর করে এগিয়ে যেতে পারে।
ভিয়েনাতে আমার সংগ্রামের দিনগুলোতে আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে শুধু ভাবাবেগ দিয়ে সামাজিক এ অদ্ভুত সমস্যার সমাধান করা যাবে না। বরং তা ভাবতে গেলে পুরো ব্যাপারটাই হাস্যাস্পদ এবং অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। তার চেয়ে এমন একটা পথ আবিষ্কার করতে হবে যা আমাদের সমাজের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক এ ক্ষয়িষ্ণু দিকের ক্ষয় রোধ করে ওপরে টেনে তুলতে পারে। সমাজের এ ক্ষুয়িষ্ণু দিকটাই একটা মানুষকে তার নিজের সিংহাসন থেকে ঠেলে নিচে নামিয়ে দিয়েছে বা দিতে সাহায্য করেছে। এবং বেকারত্বই হল তার একটি সর্বপ্রধান কারণ; যেটা মানুষকে প্রতিনিয়ত এক চরম অনিশ্চয়তার পথে এগিয়ে দিয়েছে। আর এ প্রতিনিয়ত অনিশ্চয়তাই তাকে নিচের দিকে আকর্ষণ করেছে; গভীর বা সুনির্দিষ্ট জীবনের ধারা গ্রহণ করতে দিচ্ছে না। তাদের কাপুরুষ আর জীবন সম্পর্কে উদাসীন বা অমনোযোগী করে তুলছে। এবং এ মনোভাব তাকে আত্মবিশ্বাসে স্থির থাকতে দিচ্ছে না। যখন এ আত্মপীড়ন থেকে লোকে মুক্তি পাবে, তখনই তার অন্তশক্তি এবং বহিঃশক্ত দুটো মিলিয়ে সে সমাজের এবং নিজের উন্নতির চেষ্টা করবে। হ্যাঁ, পঙ্গু ডালপালা এবং অপ্রয়োজনীয় শিকড়ের ডাল থেকে বেরিয়ে আসার এ একমাত্র পথ।
কিন্তু অস্ট্রিয়ার শাসককুলের সামাজিক দাবি দাওয়া সম্বন্ধে কোন ধ্যান ধারণা বা সামাজিক সঠিক অনুশাসনের অভাবই সমাজের এ দুষ্ট ক্ষতগুলোকে সারতে দেয়নি।
আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি সঠিক কোন জিনিসটা আমাকে বেশি আচ্ছন্ন। করেছিল? দারিদ্রতা, যেটা আমার সেদিনের সর্বক্ষণের সঙ্গী অথবা আমাকে ঘিরে থাকা লোকগুলোর বুদ্ধিমত্তা এবং সাংস্কৃতির অভাব।
সবচেয়ে অবাক ব্যাপার আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা কত তাড়াতাড়ি কুদ্ধ হয়ে ওঠে যখন এসব ব্যাপার তারা পদদলিত কোন ব্যক্তির কাছ থেকে শোনে। তারা জার্মান হোক, বা না হোক। এ অবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভে তারা ফেটে পড়ে, কিন্তু তাদের সেই ঘৃণা মিশ্রিত ক্ষোভের বেশির ভাগটাই ভাবালুতায় ভরা ফানুস মাত্র।
কিন্তু ক’জন সত্যিকারের আত্মবিশ্লেষণ করে? অবশ্য ভাবালুতার বাষ্পে তা সম্ভবও নয়। ক’জন বুঝতে চেষ্টা করে যে পিতৃভূমির যে অংশটার তারা অংশীদার, তার সাংস্কৃতিক এবং প্রাকৃতিক সমৃদ্ধির দিকটাকে। আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কি একবারও ভাবে যে পিতৃভূমির সমাজের এমন একটা উজ্জ্বল দিক থাকা উচিত যা নিয়ে তারা গর্ব করতে পারে।
একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, যে অন্যান্য দেশের শ্রমিক শ্রেণীও কম দেশপ্রেমিক নয়। যদি সেটা স্বীকার করে নেওয়া যায় তবু আমাদের অবহেলাকে গুরুত্ব না দিয়ে উপায় নেই। কিন্তু ব্যাপারটা এ রকম নয়। আমরা যেটাকে বলি অন্ধ জাতীয়তাবাদী, ফ্রান্সের মহত্বের পরিপূর্ণ বিকাশে সেটাই তাদের সভ্যতা। শুধু সামনে একটা আদর্শ বা লক্ষ্যকে দাঁড় করিয়ে রেখে ফরাসী ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া হয় না। শিক্ষা বলতে তাদের দেশের বিস্তারিত সংস্কৃতি এবং রাজনৈতিক পটভূমিকা শেখা, এবং তা শেখানো হয় অতি বিস্তারিতভাবে।
এ ধরনের শিক্ষার পটভূমি বিরাট হওয়া উচিত এবং বারবার শিখিয়ে মনের গভীরে তার অনুপ্রবেশ ঘটানো চাই।
আমাদের ক্ষেত্রে আমরা যে শিক্ষার সেই দিকটাকে উপেক্ষা করে চলেছি শুধু তাই নয়, যারা ভাগ্যবলে স্কুলের দৌলতে একটু আধটু শিক্ষা পাচ্ছে তাদের মনটাও সম্পূর্ণ বিকৃত করে দেওয়া হচ্ছে। বিষাক্ত ইঁদুর প্রতিনিয়ত আমাদের রাজনৈতিক দেহে বিষ ছড়িয়ে চলেছে। হৃদয় এবং সেই স্মৃতিশক্তিকে সেই বিষে আচ্ছন্ন করে দিয়ে এ বিশাল জনতাকে দুঃখ দুর্দশার চরমে নামিয়ে দিচ্ছে।
পাঠকগণকে নিচের একটা দৃশ্য কল্পনা করতে অনুরোধ করি।
মাটির নিচের আর্দ্র দুটো ঘরে একজন শ্রমিক তার পরিবার নিয়ে বাস করে, সর্বসাকুল্যে তারা সাতজন। ধরে নেওয়া যাক পরিবারের একজন হল তিন বছরের একটা ছেলে। এ বয়সে বাচ্চারা যা দেখে এবং শোনে, তাদের মনে তা গভীরভাবে দাগ কেটে বসে। প্রতিভাশালী লোকের ক্ষেত্রে এ বয়সের ঘটনা এমনভাবে মনের মধ্যে রেখাপাত করে যে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তা তাদের স্মরণে থাকে। সুতরাং এ জীবনের সংকীর্ণতা এবং এতটুকু পরিবেশে অতো লোকের ভিড় তার মনে নিশ্চয়ই কোন সুখস্মৃতির ছবি আঁকে না। এ পরিবেশে তাই ঝগড়া আর পরস্পরের বোঝাপড়ার অমিল তো থাকবেই। এতটুকু জায়গায় যেখানে পাশাপাশি শোওয়াও অসম্ভব; ওপর নিচে শোওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। ছোট ছোট অমিলগুলো, যেগুলো ঘরে বেশি জায়গা থাকলে পরস্পরের কাছ থেকে একটু দূরে সরে বসতে পারলে সহজেই মিটে যায়; এখানে সেগুলোই পুরনো রোগের মত দেখা দেয়। ছোটদের ক্ষেত্রে তারা পরস্পর ঝগড়া করলেও ঝগড়া সহজে মিটে যায়। এবং অল্পক্ষণের মধ্যে তা ভুলেও যায়। কিন্তু বড়দের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটাই অন্যরকম হয়ে দেখা দেয়। প্রাত্যহিক ঝগড়াতে যে নির্দয়তা থাকে, সেটাই সংসারের সব শান্তি ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেয়। এগুলো ছেলেপেলেদের জীবনে প্রতিক্রিয়াও কম করে না। কারোর যদি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকে, তার পক্ষে ব্যাপারটা বোঝা সম্ভব। যখন মত্তমাতাল অবস্থায় ঘরে ফিরে স্বামী স্ত্রীকে দৈহিক নির্যাতন করে, সমস্ত পারিবারিক প্রতিক্রিয়া ব্যাপারটাতে যা হয়, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া বোঝা এটা সম্ভব নয়। বছর ছয়েক বয়স হলে বাচ্চারা তো দূরের কথা, এসব ঘটনাতে বড়রাও স্থির থাকতে পারে না। বিষাক্ত তত্ত্বে জারিত, পেট ভরে খেতে না পাওয়ায় অপুষ্ট শরীর আর মস্তিষ্ক ভরা কীট নিয়ে তারা ঢেকে গিয়ে প্রাইমারী স্কুলে। এরাই দেশের ভবিষ্যত নাগরিক। অতিকষ্টে সেখানেই তারা যতটুকু পারে পড়াশোনা করে। বাড়িতে তো পড়াশোনা করার না আছে জায়গা, না পরিবেশ। উপরন্ত বাবা মা সর্বক্ষণ স্কুলের শিক্ষকদের সমালোচনায় মুখর। বিশেষ করে এ পরিবেশে যেসব সমালোচনা হয়, তার আওতা থেকে কিছুই বাদ পড়ে না। স্কুল থেকে শুরু করে গভর্নমেন্ট পর্যন্ত। ধর্ম, আদর্শ, রাষ্ট্র কোন কিছু সম্পর্কেই এখানে গঠনধর্মী কোন আলোচনা হয় না। যখন চৌদ্দ বছর বয়সে সে স্কুল ছেড়ে বেরয়, তখন সুশিক্ষার বদলে এ জিনিসগুলোই নড়াচড়া করে বেশি।
জীবনের এ সন্ধিলগ্নে মহৎ আদর্শের প্রতি মন ধাবিত না হয়ে মানব জীবনের অন্ধকার দিকটার প্রতিই মন আকৃষ্ট হয় বেশি। পনেরো বছর বয়সে সেই তিন বছরের ছেলেটা সব কিছুর বিরুদ্ধে জেহাদ শুরু করে। জীবনের নোংরা এবং কদর্যময় দিকটার প্রতি-ই তার আকর্ষণ গড়ে উঠে; চিন্তাধারার উঁচু দিকটার প্রতি তখন তার চরম অনীহা। মানসিক ঠিক এ অবস্থাতে সে স্কুলে গিয়ে প্রবেশ করে।
তার জীবনের ছোটবেলায় দেখা পিতার দৈনন্দিন খাত ধরেই বয়ে চলে। ভবঘুরে হয়ে সারাটা দিন রাস্তায় রাস্তায় কাটিয়ে ঘরে ফেরে। আর সেই অর্ধমৃত জন্মদাতার উদ্দেশ্যে গালাগাল ছোড়ে। শুধু তাই নয় অভিশাপ দেয় ঈশ্বর এবং এ পৃথিবীটাকেও; শেষমেষ গিয়ে ঢেকে অল্প বয়স্ক ছেলেদের শুদ্ধিকরণের জন্য তৈরি জেলখানায়। বাকি যেটুকু ছিল তা ওখানেই পূর্ণতা পায়। এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ওদের ভেতরে দেশপ্রেমের অভাব দেখে সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে।
দিনের পর দিন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় দেখে আসছে থিয়েটার, সিনেমা; নোংরা সাংবাদিকতা এবং কদর্য বইপত্রগুলি জনতার মধ্যে বিষ ছড়িয়ে চলেছে। তবু ওরা আশ্চর্য হয় যখন দেখে যুবক সম্প্রদায়ের আদর্শ এত নিচু বা দেশপ্রেম বলতে কিছু নেই। আসলে ছোটবেলা থেকে যে মানসিকতা নিয়ে এ ছেলেগুলো বেড়ে ওঠে, বড় হয়ে সিনেমা, থিয়েটার এবং সাংবাদিকতায় তারই প্রতিফলন দেখতে পায়। এ যেন আগুনের সঙ্গে ঝড়ের হাওয়া এসে ফু দেওয়ার মত অবস্থা।
আমি কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছিলাম। যেটা আগে আমার ধারণায় ছিল না, সেই ব্যাপারটা এরকম;
উন্নত সমাজ গড়ে তুলতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন মানুষের ভেতরে দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবাদী আদর্শ জাগরিত করা। যা ছাড়া সমাজকে কিছুতেই ওপরে টেনে তোলা যাবে না। কিন্তু সেটা করতে প্রথমেই শিক্ষা এবং পারিবারিক পরিবেশের আমূল পরিবর্তন দরকার। প্রত্যেকের সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক সচেতনতারও প্রয়োজন; সর্বোপরি দেশের রাজনৈতিক পটভূমিকাও মহৎ হওয়া চাই একমাত্র তাহলেই সে দেশের নাগরিক হিসেবে গর্ব অনুভব করা যাবে। মানুষ যাকে ভালবাসে, তারই জন্য যে সংগ্রাম করতে পারে; আর যেটাকে সে শ্রদ্ধা করে, তাকেই সে ভালবাসতে পারে। আর শ্রদ্ধা করার জন্য সেই বিষয়টা সম্পর্কে পুরো না হলেও কিছুটা জ্ঞান থাকা আবশ্যক।
যেইমাত্র সামাজিক সমস্যায় আমার উৎসাহ আসে, সঙ্গে সঙ্গে তার ভিত্তি সম্পর্কে বিচার বিবেচনা শুরু করি। নতুন আর একটা অনাবিষ্কৃত জগতের পর্দা চোখের সামনে থেকে সরে যায়।
১৯০৯-১০ সালে আমার অবস্থা অনেকটা ভাল অর্থাৎ কায়িক শ্রমের কাজ করে আর আমাকে পেট ভরাতে হয় না। আমি তখন স্বাধীনভাবে ড্রাফটসম্যান এবং জল রঙের অংকন শিল্পী হিসেবে যা রোজগার করি তাতে পেটে ভরবার মত রুটি কেনার সামর্থ্য হয়েছে। এবং সেই রোজগারে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি। যদিও যথেষ্ট রোজগার নয়, তবুও পেশাটাকে আমি ভালবাসি। আমাকে ভবিষ্যত উৎসাহ দেয়। তদুপরি সন্ধ্যেবেলায় যখন আমি ঘরে ফিরে আসি, আগেকার মত অতো পরিশ্রান্ত হই না। আগে যখন আমি বাড়ি ফিরতাম তখন পড়াশোনা করার মত অবস্থা আর থাকত না। শরীরটাকে কোনরকমে বিছানায় ছুঁড়ে দিতে পারলে বেঁচে যেতাম। আমার বর্তমান কাজকর্ম ভবিষ্যতের পেশাভিত্তিক। সর্বোপরি আমি আমার কর্মসময়ের নির্ধারক, এবং নিজের মত অনুযায়ী সেই কাৰ্যসূচি পরিবর্তন বা সময় ভাগ করাও আমার হাতে। আমি ছবি আঁকতাম পেট ভরাবার জন্য, এবং পড়াশোনা করতাম, পড়াশোনা করতে ভালবাসতাম বলে।
এভাবে সামাজিক সমস্যাগুলোর পুঁতিগত দিকটা বুঝতে পারি, যাকে সাহায্য করে দিনের পর দিন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। যে সমস্ত বইপত্র এ বিষয় নিয়ে লেখা, প্রায় সবই আমি জোগাড় করে নিয়ে পড়তাম। শুধু পড়া নয়; রীতিমত চিন্তাও করতাম সেগুলো নিয়ে। সেজন্যই লোকে আমাকে খামখেয়ালী বলে ভাবত।
সমাজ সংস্কার ছাড়া আমি সাগ্রহে আর্কিটেকচার বিষয়ে পড়াশোনায় ঝাপিয়ে পড়ি। পাশাপাশি মনোনিবেশ করি সংগীত চর্চায়। যেটা আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করতাম আর্টের রানী। আর সবচেয়ে বড় কথা এ ব্যাপারে আমার যেমন উৎসাহ ছিল, আনন্দও পেতাম প্রচুর। আমি সারারাত ধরে এমন কি ভোর হওয়া পর্যন্ত এ বিষয়ে চর্চা বা পড়াশোনা করতাম। এবং দিনে দিনে আমার আত্মবিশ্বাসও দৃঢ় হয়। সময়ে আমার স্বপ্ন সফল হবে; হয়তো বা তারজন্য আমাকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হতে পারে। আমি এখন সুনিশ্চিত যে একদিন বড় স্থপতি শিল্পী হব।
আমার পেশাগত পড়াশোনার পাশে পাশে রাজনীতি সম্পর্কেও পড়াশোনা করতে শুরু করি। কিন্তু রাজনীতি বিষয়টাই আমার মনে তেমন একটা গুরুত্ব পায় না। বরং ব্যাপারটা সম্পর্কে আমার তখনকার ধারণা যে প্রতিটি চিন্তাশীল লোকের রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রাথমিক কর্তব্য। যাদের পারিপার্শ্বিক জগতটার রাজনীতি সম্বন্ধে জ্ঞান নেই, তাদের আলোচনা বা সমালোচনার কোন অধিকারই নেই। রাজনীতি সম্পর্কে আমি যথেষ্ট পড়াশোনা করি, এবং বলতে দ্বিধা নেই পড়াশোনা বলতে তথাকথিত বুদ্ধিজীবিরা যা বোঝে, আমার কাছে তা ছিল অন্য।
আমি এমন অনেককে জানি যারা বইয়ের পর বই, পাতার পর পাতা পড়ে চলে, তবু আমি তাদের পাঠক বলি না। হয়ত বা তারা অনেক পড়ছে। এমনকি তাদের কোন বইটা প্রয়োজনীয় আর কোনটা অপ্রয়োজনীয় সেটুকু তফাৎ করার মত ক্ষমতা নেই। সুতরাং তাদের অবস্থা আগেরটা পড়ে তা পরেরটা ভোলে; তারপর আবার সেটা পড়ে। আর নইলে সমস্ত ব্যাপারটাই অপ্রয়োজনীয় মাল বোঝাই জাহাজের মত মাথা ভারী করে। পড়াশোনা ব্যাপারটা শেষের জন্য নয়; বরং শেষের দিকে পা বাড়াবার প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। একটা মূল উদ্দেশ্যই হল প্রত্যেকের ভেতরে যে সুপ্ত প্রতিভা বা বিশ্বাস ঘুমিয়ে আছে তাকে জাগিয়ে তোলা। দৈনন্দিন রুটির রোজগার অথবা বড় কাজ করার বাসনা— একমাত্র পড়াশোনাই এর রসদ এবং উৎসাহ জোগাতে পারে। এগুলোই হল পড়াশোনা করার প্রথম উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হল, যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি সেটা সম্পর্কে পড়াশোনাই সম্যক জ্ঞান আমাদের দিতে পারে। উভয়ক্ষেত্রেই সমস্ত অধীত বিষয় মস্তিষ্কে জড়ো করে রাখার প্রয়োজন নেই। পড়াশোনার মাধ্যমে যে ছোট ছোট জ্ঞান আহরিত হয়, সেটা মোজাক করা মেঝেতে পাথরের মত গেঁথে রাখা উচিত। যাতে ভবিষ্যতে সাধারণ জ্ঞানের পরিপূর্ণতার জন্য সঠিক সময়ে টুকরোটা সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। নইলে অধীত বিষয়গুলো প্রয়োজনের সময়ে শুধু গোলমালের সৃষ্টিই করবে; এগুলো শুধু অপ্রয়োজনীয় নয়, প্রয়োজনের সময়ে বিপথগামীও করতে পারে। কারণ সে তো নিজেকে সব সময় বিদ্বান বলে ভাববে; মনে করবে জীবনের অনেকটাই বুঝি সে দেখে ফেলেছে। সে তখন আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। সে মনে করে জীবনে সত্যের দিকে এগোচ্ছে, কিন্তু সত্যি বলতে কি এগুলো তাকে সত্যিকারের জীবন থেকে দূরেই সরিয়ে দেয়। যদি না তাকে শেষজীবনে স্যানিটোরিয়াম বা রাজনীতি গ্রহণ করে পার্লামেন্টে জীবন পাড়ী দিতে হয়।
এসব লোকেরা জীবনে যখন সুযোগ আসে তখন তাদের বই পড়া বিদ্যা কাজে লাগাতে সক্ষম হয় না। বিশেষ করে তার মানসিক গঠনটাই তো দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, তার জন্য তৈরি নয়। মাথায় হয়তো বা বোঝাই বই পড়া বিদ্যা জমা হয়ে থাকতে পারে; কিন্তু ভাগ্যক্রমে যদি একদিন হঠাৎ ডাক পড়ে যে সে বিদ্যা কাজে লাগাও কোন একটা বিশেষ কাজের জন্য; কিন্তু কোন বইয়ের কোন অধীত পৃষ্ঠাটাকে ঠিক সেই সময় সেই কাজে লাগাতে হবে তা বলে না দিলে বেচারা এত পড়াশোনা করেও শুধু হাতড়ে মরবে। মনের এ উত্তেজক অবস্থায় সে হয়ত মন হাতড়ে ঘটনার সাদৃশ্য কিছু খুঁজে বেড়াবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে হয়ত বা দেখা যাবে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছে।
এ যদি সত্যিকারের অবস্থা হয়, তবে আমাদের দেশের পার্লামেন্টের যারা তাবড় তাবড় নায়ক, তাদের কাছ থেকে রাজনীতির ব্যাপারে কতটুকু আশা করতে পারি। আসলে তারা তাদের কথার জাল বিস্তার করে, খিস্তি খেউড় করে আর ছল চাতুরীতে সবাইকে ভোলায়।
অপরদিকে পঠিত বিদ্যা যে জ্ঞান সম্যকরূপে আহরণ করে, তা বই, জার্নাল বা বিজ্ঞাপনলিপি যা থেকেই হোক প্রয়োজনে তৎক্ষণাৎ তা স্মরণ করে সেটা কাজে লাগাতে পারে। যেটা সে পড়েছে সেই বিষয়টা মনের মধ্যে এমনভাবে গেঁথে যায় যে সেটা শুধু মানসিক চিন্তাধারটাকেই সঠিক পথে চালনা করে না, মনটাকেও উদার করতে সাহায্য করে যাতে সেটা সঠিক জায়গায় ঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারে। হঠাৎ কোন বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি হয়ে পড়লে স্মৃতির পৃষ্ঠা হাতড়ে সেই বিশাল জ্ঞান সন্দ্র থেকে মুক্তাটা তুলে এনে জায়গা মত বসিয়ে দিতে পারে। এ পড়াশোনার কিছু অর্থ হয় বা এর কিছু মূল্য আছে।
বক্তা— যার হাতের কাছে খবর তৈরি নেই প্রতিপক্ষের বক্তব্য খণ্ডানোর মত, তার এ বিদ্যার কোন অর্থ হয় না— তা তার নিজের যুক্তি যত ধারালই হোক না কেন? প্রত্যেক আলোচনাতেই তার স্মৃতি তাকে লজ্জায় ফেলে হারিয়ে দেবে। প্রতিপক্ষের বক্তব্যকে বিধ্বস্ত করার মত যুক্তি সে খুঁজে পায় না সে সময়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত বক্তা তার নিজের যুক্তির জাল বিস্তার করে, ব্যাপারটা তখন ঘোরালো হয় না। কিন্তু ব্যাপারটা গুরুতর হয়ে ওঠে কোন বিশেষ জনসাধারণের ব্যাপার হলে, যখন সে ভাবে সব কিছুই তার জানা, আসলে সে কিছুই জানে না।
ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনা আমি সঠিক পথে করতাম। উপরন্তু আমি ভাগ্যবান যে আমার স্মৃতিশক্তি ছিল প্রখর এবং বুদ্ধিমান ছিলাম, যা পঠিত বিষয়কে স্মরণে রাখতে এবং জায়গা মত ঠিক মত প্রয়োগ করতে সাহায্য করত। সেইদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমার ভিয়েনার প্রবাস জীবন আমার পক্ষে শুধু প্রয়োজনীয়ই ছিল না, উপকারীও ছিল বটে। আমার দৈনন্দিন কাজই ছিল বিভিন্ন সমস্যাগুলোকে নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করা। আমি যার জন্য বাস্তব অবস্থাগুলোকে সূত্রের মাধ্যমে বা সূত্রগুলোকে বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে পারতাম। সুতরাং প্রতি বিষয়ে একদিকে পণ্ডিতাভিমানী তত্ত্ব আর অপরদিকে বাস্তব অবস্থায় ওপরটা দেখার বিপদের হাত থেকে বেঁচে গেছি।
প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতায় আমি মনস্থির করি দুটো প্রশ্নের ব্যাপারে তত্ত্বের গভীরে আমাকে প্রবেশ করতে হবে; বিশেষ করে সামাজিক সমস্যার বাইরে।
এটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে সঠিক কখন আমি মার্কস্ মতবাদের চরিত্র সম্পর্কে পড়াশোনা বা বিচার বিশ্লেষণ শুরু করি; তবু এটা সত্য নয় যে এ মার্কসীয় সমস্যা নিয়ে আমাকে খুব বেশি রকম মাথা ঘামাতে হয়েছে।
আমার যৌবনকালে সামাজিক গণতন্ত্র সম্পর্কে আমার যে ধ্যান-ধারণা ছিল তা অতি সামান্য; এবং সেই সামান্য অংশের ভেতরে বেশিরভাগটাই ভুল ধারণা। সত্যি বলতে কি বিশ্বজোড়া দুঃখের এটা একটা কারণ, তবু গোপন ভোটদানের পদ্ধতি আমাকে সন্তুষ্ট করেছিল। আমার বুদ্ধি এবং বিশ্লেষণী শক্তি যেন আমায় তখন বুঝিয়েছিল যে এ পথই হাবুবুর্গ শাসককে দুর্বল করে দেবে; যাকে আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করতাম। যদিও এ পদ্ধতিতে দানুবিয়ান রাজ্যের হয়ত বা অস্তিত্ব থাকত না। এমন কি অস্ট্রিয়ার জার্মান সাম্রাজ্যের অস্তিত্বও হয়ত বা বিপন্ন হয়ে পড়ত, কারণ শ্লাভদের রাজনৈতিক সাংগঠনিক দক্ষতা কতদূর ছিল তা মোটেই প্রশ্নাতীত নয়। সুতরাং আমার আগ্রহ ছিল এমন সব সংগ্রাম যাতে এসব শাসককুল পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে দশলক্ষ লোক তাদের নিজস্ব জার্মান প্রকৃতি ফিরে পায়। পার্লামেন্টে যত বেশি হট্টগোল হবে, এ ব্যবিলোনিয়ান সাম্রাজ্যের পতন তত আসন্ন হয়ে উঠবে। তার মানে অস্ট্রিয়ার জার্মানদের মুক্তি। একমাত্র তখনই তারা তাদের মাতৃভূমির সঙ্গে একত্র হতে পারবে।
সত্যিকারের সোশ্যাল ডেমোক্রেটদের প্রতি আমার এতটুকু বিরাগ বা বিতৃষ্ণা ছিল। কিন্তু আমার অক্ষমতার জন্য আমি বিশ্বাস করতাম যে শ্রমিক শ্রেণীকে ওপরে তোলার এটাই একমাত্র পথ; এটা একটা প্রধান কারণ যে জন্য আমি সোশ্যাল ডেমোক্রেটদের স্বপক্ষেই ওকালতি করে এসেছি, বিপক্ষে নয়। সোশ্যাল ডেমোক্রেট মুভমেন্টের যে দিকটা আমার ভাল লেগেছে তা হল অস্ট্রিয়ায় বসবাসকারী জার্মানদের জন্য ওদের সংগ্রাম, তাদের শ্লাভ কমরেডদের প্রতি সহানুভূতি। কিন্তু তখন আমি বুঝতে পারি নি, যে যতদিন পর্যন্ত তাদের দিয়ে কাজ হবে, সোশ্যাল ডেমোক্রেট ততদিন পর্যন্ত তাদের এই চোখে দেখত।
সুতরাং সতের বছর বয়সে মার্কসইজম শব্দটাই আমার কাছে খুব একটা পরিচিত ছিল না, বরং সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি যাকে সোশ্যালিজিমের সমর্থক বলেই ধরে নিয়েছিলাম। সেইজন্যই বোধহয় ভাগ্য আমাকে হঠাৎ বজ্ৰমুষ্ঠাঘাতে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে এটা জনসাধারণকে ধোঁকা দেবার এক অতি উত্তম পদ্ধতি।
অবশ্য এ সময় সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সঙ্গে আমার সংস্রব বলতে ওদের গণ মিটিংয়ে আমি স্রেফ দর্শক ছিলাম। পার্টির নীতি এবং তাদের সামাজিক শিক্ষা সম্পর্কে পার্টি নেতৃত্বের সামান্যতম ধ্যান-ধারণাও আমার ছিল না। হঠাৎ আমাকে তাদের তথাকথিত শিক্ষা বা দর্শনের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এভাবে কয়েক দিনের মধ্যে আমি সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির স্বরূপ বুঝতে পারি, স্রেফ যে পরিবেশে আমার দিনগুলো কাটত তার জন্য। অন্যথায় এ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির স্বরূপ বোঝার জন্য আমাকে হয়ত বা একটা পুরো যুগ কাটাত হত। আর সামাজিক উন্নতি এবং প্রেমের ছদ্মবেশে পরস্পর এ অতি বাস্তব সংক্রামক ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ত দেশে বিদেশে; এবং কালে এ সংক্রামক ব্যাধিকে রোধ করা না গেলে পৃথিবীর বুক থেকে মানুষ জাতিটাকেই হয়ত বা নিশ্চিহ্ন করে দিত।
বাড়িঘর নির্মাণের ব্যাপারে জড়িত থাকাকালে আমি প্রথম সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সংস্পর্শে আসি।
আমি যখন কাজ শুরু করি তখনকার অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। জামা-কাপড়ের অবস্থা শোচনীয়। আমি তখন অবশ্য আমার কথাবার্তায় অত্যন্ত সতর্ক এবং ব্যবহারেরও প্রচণ্ড রকমের সংযত হয়ে চলতাম। আমি তখন আমার বর্তমানের দুরবস্থা এবং ভবিষ্যতের ভাবনা, নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলাম যে বর্তমান পরিবেশ নিয়ে মাথা ঘামানোর মত না ছিল মানসিক অবস্থা, না ফুরসৎ। আমাকে কাজ করতে হত নেহাত-ই পেটের দায়ে এবং পড়াশোনা করার তাগিদে। ভবিষ্যতের এগিয়ে থাকার পথ ধরে অবশ্যই এ পরিক্রমা আমার ধীরগতিতে ছিল; যদি আমার কাজের তৃতীয় বা চতুর্থ দিনে বিশেষ ঘটনা ঘটত, তবে হয়ত বা বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে মেলামেশা করতাম না। এ সময় আমার ওপরে আদেশ হয় ট্রেড ইউনিয়নে যোগ দেবার।
তখন অবশ্য ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কে আমার জ্ঞান বলতে কিছু ছিল না। সত্যি বলতে কি এর প্রয়োজনীয়তা বা অপ্রয়োজনীয়তা কিছুই বুঝতাম না। কিন্তু আমাকে যখন বলা হল যে ট্রেড ইউনিয়নে আমাকে নাম লেখাতে হবে, আমি সোজাসুজি প্রত্যাখ্যান করলাম। প্রত্যাখ্যানের কারণ হিসেবে আমি বললাম, যে বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান নেই, সে বিষয়ে নিজেকে আমি কখনই জোর করব না। সম্ভবত এ কারণটাই আমাকে আমার সত্যিকারের পথ থেকে বিচ্যুতি করেনি। ওরা বোধহয় ভেবেছিল কয়েকদিনের ভেতরে আমার চিন্তাধারা বদলে আমি ওদের বাধ্য হয়ে উঠব। কিন্তু ওরা এটা ভেবে যে প্রচণ্ড রকমের ভুল করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। সপ্তাহ দুয়েক পরে আমি বুঝতে পারি, প্রথমে রাজী যদি হয়েও যেতাম, কিন্তু বর্তমানে রাজী হওয়া অসম্ভব। এ দুই সপ্তাহে আমি আমার সহকর্মিদের আরো ভালভাবে বুঝতে পারি এবং নিজের মনটাকে এমন দৃঢ়ভাবে স্থির করি যে পৃথিবীর এমন কোন শক্তি নেই যা আমাকে ট্রেড ইউনিয়ানে যোগ দেওয়াতে পারে। আসলে এখন আমি আমার অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের স্বরূপটা ভালভাবেই বুঝতে পেরেছি।
বলাবাহুল্য আমার চাকরির প্রথম দিনেই ব্যাপারটাতে তখন আমার বিরক্তি এসে গেছে। দুপুরবেলা আমার কয়েকজন সহকর্মি শ্রমিক কাছের গুড়িখানায় গিয়ে হাজির হত, আর অন্যেরা সেই নির্মীয়মান বাড়ির একাংশে বসে তাদের মধ্যাহ্নের খাওয়া-দাওয়া সারত; বেশিরভাগ খাওয়া-দাওয়া বলতে বোঝাতে শুকনো এক আধ টুকরো রুটি। অবশ্য এরা সবাই সংসারী, বিবাহিত। তাদের স্ত্রীরা ভাঙা পাত্রে দুপুরের খাওয়ার জন্য স্যুপ নিয়ে আসত। সপ্তাহের শেষের দিকে শুঁড়িখানায় যাওয়ার লোক কমতে থাকত; বেশির ভাগই দুপুরের খাওয়ার জন্য নির্মীয়মান বাড়ির একাংশে ভিড় জমাত। পরে অবশ্য এর কারণটা আমি বুঝতে পেরেছি। তখন তারা রাজনীতি নিয়ে তর্কে-বিতর্কে মেতে থাকত।
আমি বাইরে কোথাও বসে দুধের বোতলের সঙ্গে রুটির টুকরো চিবোতাম আর যে পরিবেশে আমি বর্তমানের দিনগুলো কাটাচ্ছি তার দুর্ভাগ্যের কথা মনে মনে চিন্তা করতাম। যদিও আমি ওদের কথাবার্তা বেশিরভাগই শুনতে পেতাম। আমার ধারণা, দলে টানবার জন্য ওরা ইচ্ছে করেই আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে আলোচনাগুলো উঁচু স্বরে করত। কিন্তু আসলে ওদের কথাবার্তা শুনে আমার মনটা আরো বেশি বিষিয়ে উঠত। সেই সমালোচনায় সবকিছুরই নিন্দা চলত–বিশেষ করে জাতির উদ্দেশ্যে; কারণ তা নাকি খালি বড়লোকদেরই স্বার্থ দেখেছে। (এ কথাটা আমাকে যখন তখন প্রায়ই শুনতে হত।) ফাদারল্যান্ড অর্থাৎ পুরো দেশটাই নাকি বুর্জোয়াদের হাতে এবং তারা ইচ্ছে মত শ্রমিক শ্রেণীর ওপর নিরঙ্কুশ শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। শাসক স্কুলের কাজই নাকি প্রলেতেরিয়া গোষ্ঠীকে নিচে ঠেলে ফেলে দেওয়া; ধর্ম তো শুধু লোকেদের ফাঁকি দিয়ে প্রতারণা করার জন্য; আদর্শ-টাদর্শ কথাগুলো স্রেফ লোকেদের বোকা বানানো আর মেয়েদের মত জনতাকে সুবোধ রাখার জন্য। এমন কিছু বিষয়বস্তু বাদ থাকত না যা তারা আলোচনার নোংরা কাদায় টেনে না নামাত।
প্রথমদিকে আমি চুপচাপ থাকতাম। কিন্তু এমনি মুখে কুলুপ এঁটে আর কতদিন থাকা যায়। শেষে ওদের আলোচনায় অংশ নিতে শুরু করি; এবং তাদের বক্তব্যের উত্তর দিতে থাকি। যদিও জানতাম এসবের কোন ফলই পাওয়া যাবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত আমি ওদের আলোচনার বা সমালোচনার সঠিক উত্তর দিতে পারছি, সুতরাং আমি স্থির করি ওরা যেখান থেকে ওদের জ্ঞান বুদ্ধি আহরণ করে, সেই জায়গাগুলোর খোঁজ খবর আমাকে রাখতে হবে। সুতরাং আমি বই এবং পত্র-পত্রিকার সমুদ্রে ডুবে যাই।
ইতিমধ্যে সেই নির্মীয়মান বাড়ির মধ্যে বসে আমাদের তর্ক-বিতর্ক চলতেই থাকে। দিনে দিনে তারা যেসব বিষয়ে নিজেদের বিশেষজ্ঞ বলে মনে করত, তাদের চেয়ে সেসব বিষয়ে আমার জ্ঞান অনেক বেশি বেড়ে যায়। তারপর একদিন আসে যখন আমার আহরিত জ্ঞানের ধারালো কথাগুলোকে তাদের জোরালো যুক্তি দিয়ে খণ্ডনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কিন্তু যুক্তি থাকলে তো খুঁজে পাবে। সুতরাং শুরু হয় আমাকে গায়ের জোরে ভয় দেখানো। দলের কয়েকজন নেতা আমাকে সেই চাকরি ছেড়ে দিতে আদেশ দেয় নইলে মারধোর করে তাড়াবে। আমি একা হওয়াতে গায়ের জোরে ওদের সঙ্গে পেরে উঠব কেমন করে? সুতরাং আমার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে আরো কিছু অভিজ্ঞতা ভরে নিয়ে প্রথম সুযোগেই তাদের সংস্পর্শ ত্যাগ করি।
যদিও আমি বিরক্তিতে দূরে চলে গিয়েছিলাম, তবু পুরো ব্যাপারটা আমার মনকে এত প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল যে কিছুতেই আমার পক্ষে তার দিকে পেছন ফিরে থাকা সম্ভব হয়নি। পুরো ব্যাপারটা নিজেই চিন্তা করতে বাধ্য হয়েছি। রাগ পড়ে এলে আবার আমার মধ্যেকার একগুঁয়েমিটা ফিরে আসে এবং যে কোন মূল্যের বিনিময়ে আমি আবার বাড়ি তৈরির কাজে ফিরে আসার জন্য মনস্থির করি। এ চিন্তাধারাটা কয়েক সপ্তাহ পরে আরো বেশি দৃঢ় হয়, কারণ সঞ্চয় বলতে স্বল্প যে কয়েকটা টাকা ছিল, ইতিমধ্যেই তা খরচ হয়ে গেছে। ক্ষুধা তার নির্মম থাবা আবার হেনেছে আমার ওপর। অন্য কোন রাস্তাও আমার সামনে খোলা নেই। কাজ খুঁজে পেলেও আমাকে আবার তা ছেড়ে দিতে হয়। কারণ সেই আগেকার অবস্থা।
তখন আমি আত্মবিশ্লেষণ শুরু করি। এ মানুষগুলো কী মহৎ মানুষের পর্যায়ে পড়ে উত্তরটা রীতিমত চাঞ্চল্যকর। যদি উত্তর হয়— হঁা, তবে এত বিপদ এবং আত্মত্যাগ নিয়ে এ ইতর শ্রেণীর জন্য সগ্রাম করা অনর্থক। অপরদিকে যদি উত্তর হয় না, তবে এ লোকগুলোর জাতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার যোগ্যতা একেবারেই নেই। অর্থাৎ আমাদের জাতি সত্যি তা হলে গরীব। সেই দ্বিধাপুর্ণ মানসিক দিনগুলোয় গভীর মনসংযোগ দিয়ে মানস চোখে আমি যেন দেখতে পাই ক্রমাগত বেড়ে চলা এ লোকগুলোকে জাতির উন্নতির পথে হিসেবে আনা কোনরকমই সম্ভব নয়।
কয়েকদিন পরে আমার মানসিকতা সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে মোড় নেয়। রাস্তা দিয়ে যেতে দেখি কিছু ভিয়েনার শ্রমিক বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। আমি প্রায় ঘন্টা দুয়েক স্থির নিশ্চিতভাবে সেই মনুষ্যরূপী ড্রাগনদের দেখি। যখন জায়গাটা পরিত্যাগ করে আমার বাড়ির দিকে রওনা হই, তখন মনটা হতাশায় ভরে ওঠে। যেতে যেতে একটা তামাকের দোকানে শ্রমিকদের সংবাদপত্র নজরে আসে। সংবাদপত্রটির নাম আরবাইটার ঝাইটুঙ বা শ্রমিকদের মুখপাত্র। এটাই হল পুরনো অস্ট্রিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির মুখপত্র। সে সস্তা চায়ের দোকানে যেখানে সাধারণ মানুষ ভিড় করত, সেখানে মাঝে মাঝে আমিও যেতাম এ পত্রিকাটা পড়ার জন্য। দোকানদার এ একটা পত্রিকাই রাখত। কিন্তু কখনই কয়েক মিনিটের বেশি এ কদর্য সংবাদ পত্রটায় আমি চোখ বোলাতে পারিনি; আসলে পত্রিকাটার মূল সুরটাই কেমন যেন এক বিশ্রী গন্ধে ভরা। কিন্তু সেদিনকার দেখা বিক্ষোভ আমার মনে যে হতাশার সৃষ্টি করেছিল, সেটাই যেন আমাকে বারবার পত্রিকাটা কিনে খুঁটিয়ে পড়ার তাগাদা অন্তর থেকে দিচ্ছিলো। সুতরাং পত্রিকাটা কিনে আমি বাড়ি গিয়ে সমস্ত সন্ধ্যে ধরে পড়ি। নজর এড়ায় না যে কতগুলো মিথ্যা পত্রিকাটা সত্য বলে চালাচ্ছে।
এখন আমি অন্যান্য বইয়ের থেকে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির দৈনিক পত্রিকাগুলো কিনে পড়ে সহজেই ওদের সত্যিকারের রাজনৈতিক দর্শনের চরিত্রটা অনুধাবন করতে পারি।
দুটো সত্যের মাঝখানের ফরাকটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি পত্রিকাগুলো যদিও মুখে স্বাধীনতা, শ্রমের মর্যাদা এবং জীবন সম্পর্কে বড় বড় শব্দ বসিয়ে অবতারের ভঙ্গিতে মানুষকে আশ্বাস দিত; কিন্তু এটা পাঠকদের ধোঁকা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। অপরদিকে মানুষের লোভটাই নির্দয়ভাবে প্রকট হয়ে উঠত। কোন কিছুরই সত্যিকারের ভিত্তি তাতে ছিল না, শুধু মানুষকে প্রতারণা করা ছাড়া। এ সাংবাদিকতা সত্য সংবাদ মোচড় দিয়ে ঘুরিয়ে এমনভাবে পরিবেশন করত যাতে সত্যিকারের সংবাদ বোঝা কারোর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আর এ পুঁথিগত তথ্য নিয়ে মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ সম্প্রদায় যারা নিজেদের বুদ্ধিমান ভাবতো, তারা আত্ম সন্তুষ্টিতে ভুগত। এ সংবাদপত্রগুলো জনগণের কাছে মিথ্যা প্রচার ছাড়া আর কিছু নয়।
এভাবে এবং সংবাদপত্রগুলোর মাধ্যমে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির উপদেশাবলী পড়ে আমার দেশের মানুষের প্রতি আমাকে আরো বেশি আকর্ষণ করে। যেটাকে আমি প্রথমে অনতিক্রম্য গহ্বর বলে ভেবেছিলাম, পরে সেটা অনেক বেশি স্নেহ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়ায়।
একবার যখন বুঝতে পারি কী বিরাট পদ্ধতিতে ওরা জনগণের মনকে বিষাক্ত করে তুলেছে, তখন একমাত্র বোকারাই এর বলী হতে পারে। সেই বছরগুলোতে যখন আমি ক্রমে ক্রমে স্বাধীন চিন্তার জগতে পা রাখতে শুরু করেছি, তখন আমি ভালভাবেই বুঝতে শিখেছি, কি করে ওরা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির সুসমাচারের মাধ্যমে জয় লাভ করছে। এখন আমি উপলব্ধি করতে পারি কেন এবং কী উদ্দেশ্যে ভাল ভাল বই এবং সংবাদপত্র পড়া ওরা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। বিশেষ করে যে সব বই আদৌ লাল বলে গণ্য নয়। কিন্তু লাল মিটিংয়ে যোগদান করা নিষিদ্ধ হয়নি। পরিষ্কার নিষ্ঠুর বাস্তবের আলোকে আমি ভবিষ্যতকে যেন দেখতে পাই। যে ভবিষ্যত এ অসহ্য উপদেশাবলীতে কালো হয়ে গেছে।
বিরাট গনমানসকে একমাত্র তাদের দৃঢ় এবং অনমনীয় মন দ্বারাই মাপা যায়। যেমন মেয়েদের অন্তর মানস এতটা নিষ্ফলা যে কোন কারণে দোলা খায় না, কিন্তু মিথ্যা আর আবেগে তারা তাদের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত করে। শক্ত মানুষের কাছে দুর্বলরা সত্বর যেমন মাথা নোওয়ায়— ঠিক তেমনি সাধারণ মানুষ শক্ত শাসকের কাছে প্রার্থনা জানাতে ভালবাসে। যদিও সেই শাসক আবার তাদের উপদেশাবলীর আড়ালে মানসিক নিরাপত্তার আশ্বাস দেয়। কারণ সাধারণ জনতার পছন্দ সম্পর্কে কোন ধ্যান-ধারণা থাকে না। এবং সবসময় তারা ভাবে যে সমাজ কর্তৃক তারা পরিত্যক্ত। বুদ্ধির দিক দিয়ে তাদের ভয় দেখালেও তারা লজ্জিত হয় না। কারণ তারা চিন্তাতেও আনতে পারে না যে মানুষ হিসেবে তাদের স্বাধীনতা নির্লজ্জের মত তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। সুতরাং তাদের সামান্যতম সন্দেহ হয় না যে ভুল মতবাদটাই তারা স্বাভাবিক বলে মেনে নিচ্ছে। একমাত্র নির্দয় শক্তি এবং বীভৎসতার কাছেই তারা মাথা নত করে।
যদি সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসিকে সত্যিকারের শিক্ষা দিয়ে বিরুদ্ধতা করা যায় তবে সে সংগ্রাম হবে তিক্ততায় পরিপূর্ণ। তবু এ সত্যিকারের শিক্ষাই হবে চিরস্থায়ী অবশ্য যদি ঠিক একই রকম নির্দয়ভাবে সঙ্গে সেটাকে রূপায়িত করা সম্ভব হয়।
মাত্র দু বছরেরও কম সময়ে এ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির প্রকৃত শিক্ষা ও তাদের কলাকৌশল রপ্ত করে ফেলি।
আমি ওদের এ কুখ্যাত কলাকৌশল যেটা দিয়ে ওরা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে ভয় পাওয়ায় সেটা সহজেই অনুধাবন করি। এ ধরনের আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার জন্য মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কখনই মানসিক বা আধ্যাত্মিক শক্তি রাখে না। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির কলাকৌশল হল আর কিছুই নয়, একরাশ প্রজ্জলিত মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে তাদের চোখে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ভয় পাইয়ে দেওয়া, যতক্ষণ না পর্যন্ত লোকটার মানসিক শক্তি ভেঙে পড়ে এবং তাদের কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়। কারণ তখন লোকটার মনের অবস্থা এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যখন সে একটু শান্তিতে থাকতে পারলে বেঁচে যায়। কিন্তু তাদের আশা দুরাশাই হয়ে দাঁড়ায়; কখনই তাদের শান্তিতে থাকতে দেওয়া হয় না।
ওই কলাকৌশল বারে বারে পুনরাবৃত্তি করা হয়, যাতে লোকটা উন্মাদ কুকুরের পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়, ওদের কাছে নিঃশর্তভাবে আত্মসমর্পণ করে।
যদিও সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতায় শক্তির মূল্য বুঝতে শিখেছে, সেই কারণে যখনই কোন লোকের মধ্যে ব্যক্তিত্বের গন্ধ পায়, যেটা অবশ্য খুবই কম, তাকেই বশে আনতে একই পদ্ধতি প্রয়োগ করে। অপরদিকে দুর্বল মানুষগুলো মরা ইতর প্রাণী ছাড়া আর কিছু নয়, অন্ততপক্ষে মানসিক শক্তির দিক থেকে, তাদের প্রশংসা এবং উৎসাহ দিয়ে নিজেদের দলে ভেড়ায়। যে প্রতিভাধর মানুষের ইচ্ছাশক্তি থাকে না, তারাই কম ভীতিপ্রদ। যে সব বলিষ্ঠ চরিত্রের সঙ্গে বুদ্ধি যোগ দেয়, তারা বুদ্ধি এবং ইচ্ছাশক্তির জোরে নেতৃত্বের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে আসে।
সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা ভালভাবেই জানে কি করে জনগণের মনের ওপরে চাপ ফেরতে হয় যে তারাই একমাত্র শক্তির ধারক ও বাহক। এভাবে অবস্থা অনুযায়ী ধীরে ধীরে তারা তাদের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলে। একের পর এক জায়গা দখল করে। কখনো বা ভয় দেখিয়ে কখনো দিন দুপুরে ডাকাতি করে। এ শেষের পদ্ধতি ওরা প্রয়োগ করে যখন জনতার আকর্ষণ অন্য কোন বিষয় বস্তুতে নিবদ্ধ হয় এবং তা ফিরতে না চায়। অথবা যখন সাধারণ মানুষ মনে করে নগণ্য কোন ঘটনাকে ওরা বিকৃত করে বিরুদ্ধ পক্ষের চরিত্র হনন করছে।
এ কলাকৌশলগুলো মানুষের দুর্বল দিকটাকে সঠিক বিবেচনা করে অংকের মত হিসেব করে তৈরি করা হয় যাতে সাফল্যে কোন সন্দেহ না থাকে, অবশ্য যদি না প্রতিপক্ষ শেখে বিষ বাস্পের বিরুদ্ধে কি করে বিষবাষ্প দিয়ে যুদ্ধ করতে হয়। দুর্বল প্রকৃতির লোকদের প্রতিটি পদক্ষেপে বলে দিতে হয় এটা হওয়া উচিত বা উচিত নয়। আমিও অবশ্য বুঝতে শিখলাম শারীরিক ভয় প্রদর্শন দ্বারা জনতা বা একক ব্যক্তিকে দিয়ে কোন একটা উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। এ ব্যাপারে সন্দেহ নেই যে সোশ্যালিস্টরা গাণিতিক ছক কষে নিয়েছিল যে তাদের শারীরিক প্রতিক্রিয়া দ্বারা কর্মস্থলে বা কারখানায়, জামায়েতে বা গণবিক্ষোভে এ ভয় প্রদর্শন সব সময়ই সফল হবে, যদি না তার চেয়ে বেশি ভয় এবং বীভৎসতা অপরপক্ষকে দেখানো যায়। তখন অবশ্য পার্টি মরণ আর্তনাদ করে উঠবে। এ ঠান্ডা মাথায় হত্যার বিরুদ্ধে সেই শাসককুলের কাছেই আবেদন জানাবে, যে শাসককুলকে তারা স্বীকার করে না বা পাত্তা দেয় না। এ ভাবে। তারা নিজেরাই নিজেদের লক্ষ্যপথ থেকে সরে আসবে এবং নিজেদের গন্তব্যস্থল অনেক বেশি অরক্ষিত হয়ে পড়বে। তারা তখন প্রাণপণ চেষ্টা করবে উঁচু পদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে সঁড়ের মত বোকা কয়েকটাকে খুঁজে বের করতে; যারা বোকার মত চেষ্টা করবে অপরপক্ষের ভয় মিশ্রিত শ্রদ্ধা অর্জন করার, যাতে তারা তার ভবিষ্যতের বিপদ আপদের সময় সাহায্যে আসে, এবং সে তাদের বর্তমান পথের কাঁটাটাকে ভেঙে ফেলে দূরে সরিয়ে দিতে সহায়ক হবে।
এ ধরনের কলাকৌশল সাধারণ গণমানসে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া তুলবে, অনুগত বা বিরুদ্ধপক্ষ যে-ই হোক না কেন, একমাত্র তারাই বুঝতে পারবে যাদের জনতার চরিত্র ভালভাবে জানা আছে। হ্যাঁ, বইপড়া বিদ্যে নিয়ে নয়, নিকট অভিজ্ঞতা থেকে। এ সাফল্যগুলোই সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির অনুগতরা শিঙা ফুকে নিজেদের সঠিক বলে প্রচার করে বেড়ায়। অপরদিকে মার খাওয়া প্রতিপক্ষ বেশির ভাগ সময়েই নিজেদের প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে।
যতই এ শারীরিক ভয় প্রদর্শন করতে থাকে, তত বেশি সহানুভূতি আমার জেগে। ওঠে সাধারণ জনসাধারণের প্রতি, যারা ভয়েই ওদের বশীভূত।
সেই সময় যে সব পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে আমাকে পথ হাঁটতে হয়েছে তার জন্য আমি নিজেকে ধন্যবাদ দেই। কারণ এটাই আমাকে জনসাধারণের কাছে এবং জনসাধারণের প্রতি ভাবতে সাহায্য করেছে। অভিজ্ঞতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি নকল নেতৃত্ব এবং সেই নকল নেতৃত্বের বশীভূত বিপথগামী লোকগুলোকে আলাদা করতে সক্ষম হয়েছিলাম।
আমাদের উচিত এ যুপকাষ্ঠে বলি হওয়া লোকগুলোর প্রতি সহানুভূতি দেখানো। আমি এখানে কয়েকটা উদাহরণ দেব যে লক্ষণগুলোর সাহায্যে সামাজিক নিচুতলার লোকগুলোর মানসিকতা বোঝা যাবে। কিন্তু আমার লেখা চরিত্রগুলো কিছুতেই জীবন্ত হয়ে উঠবে না, যদি না আমি স্বীকার করেনি যে সেই অন্ধকার সামাজিক নিচুতলার লোকগুলোর মধ্যেই আলোর স্ফুলিঙ্গ দেখেছিলাম; তাদের মধ্যেও কয়েকজন ছিল অবশ্যই সংখ্যায় অত্যন্ত কম, যাদের আত্মোৎসর্গ এবং অনুগত মনোভাব সগ্রামের সত্যিকারের সঙ্গী হওয়ার যোগ্যতা রাখে। যারা জীবনে প্রায় কিছুই চায় না এবং যে সাধারণ পরিবেশ তাদের ঘিরে থাকে, তাতেই তারা সন্তুষ্ট; এ গুণগুলো বিশেষ করে পুরনো শ্রমিকদের মধ্যে দেখা যেত। যুবকদের মধ্যে থেকে এ বিশেষ গুণগুলো দ্রুত অবলুপ্তি পেলেও তার জন্য শহুরে পরিবেশ ও আধিপত্যই দায়ী; তবু সেই যুবকদের মধ্যেও কিছু ছিল যারা আন্তরিকভাবে একটা আদর্শকে (সেই নোংরা দৈনন্দিন জীবনে কোনরকমে বেঁচে থাকার পরিবেশের মধ্যে থেকেও) বুকের মধ্যে সযত্নে লালন পালন করত। যদি ওদের মধ্যে কেউ জনসাধারণের শত্রুদের সমর্থন করে থাকে, তবে তার একমাত্র কারণ হল সোশ্যালিস্ট আন্দোলনকারীদের কুখ্যাত মতবাদ তারা বুঝতে পারত না। এর আরো একটা কারণ হল জনসাধারণের কোন অংশই শ্রমিকদের ভাগ্য সম্পর্কে কোনরকম চিন্তা-ভাবনা করত না। আসলে সামাজিক অবস্থাটাই ছিল এ ধরনের ঘঁচে ঢালা, যাতে প্রথমে অনিচ্ছুক হলেও শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হত। শেষে এমন একদিন এল যে দারিদ্রতার ভয়ংকর হাঁ মুখ তাদের তাড়িয়ে নিয়ে গেল সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের দলে।
অসংখ্যবার বুর্জুয়া অর্থাৎ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় শ্রমিকদের মানবতার দিকে পর্যন্ত তাকায়নি, তাদের ন্যায্য দাবি দাওয়ার চরম বিরোধিতা করেছে। এ অন্যায় এবং অবিবেচনায় মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীর কোন লাভই হয়নি। কিন্তু তার ফলে সত্যিকারের সৎ শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়নের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে রাজনীতির দিকে বাধ্য হয়ে দৌড়ে গেছে।
লক্ষ লক্ষ শ্রমিক যারা প্রথমদিকে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রচন্ড বিরোধিতা করেছে; কিন্তু তাদের সেই বিরোধিতাকে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি গায়ের জোরে এমনভাবে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিয়েছে যে তারা একসময়ে বাধ্য হয়েছে নতি স্বীকার করতে। তবু আমি বলব এ পরাজয় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের চরম মুখামীর ফল। যারা শ্রমিক শ্রেণীর সমস্ত রকম ন্যায্য দাবির শুধু বিরোধিতাই করে এসেছে। এ অপরিণামদর্শিতা যেটা শ্রমিকদের উন্নতিতে বাধা দিয়েছে, কারখানায় কর্মরত আহত শ্রমিকের অস্তিত্ব বিপন্ন করেছে বা নাবালক শ্রমিককে কাজ করতে বাধা দেয়নি; মহিলা শ্রমিকদের কোনরকম নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেনি, বিশেষ করে গর্ভবতী মাদের এগুলো সম্ভবপর হয়েছে একমাত্র সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিকদের নেতাদের সাহায্যে। যারা প্রতি মুহূর্তে সুযোগ খুঁজে বেড়িয়েছে যাতে জনতাকে প্রতারিত করে নিজেদের জালে এনে ফেলতে পারে। আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তাদের নিজেদের ভুলে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছে তা কখনই সারাতে পারবে না। কারণ সামাজিক সংস্কারের সবরকম বিরোধতা করে তারা আসলে ঘৃণার বীজ বপন করেছে। এটাকেই ওরা অর্থাৎ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট্রা শ্রমিকদের স্বার্থ দেখেছে বলে দাবি করেছে।
এগুলোই হল ট্রেড ইউনিয়নগুলোর অস্তিত্ব বিপন্নের সত্যিকারের কারণ; এবং তার ফলে শ্রমিক সংগঠনগুলো সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুলেছে।
সামাজিক এ যে সমস্যাগুলো আমাকে ঘিরেছিল সেগুলো বিশ্লেষণ করে আমি চাই বা না চাই একরকম বাধ্য হই নিজেকে ট্রেড ইউনিয়নের দিকে এগিয়ে দিতে। কারণ আমি ভেবেছিলাম এগুলোও হল সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অঙ্গ বিশেষ; বলতে দ্বিধা নেই আমার এ তড়িঘড়ি মন ঠিক করা ভুল হয়েছিল। অবশ্যই পরে আমি এ ভুলটাকে বর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলাম। কিন্তু এ বিশেষ ব্যাপারে আমার ভাগ্য আমাকে শুধু বুঝিয়েই দেয়নি; সেই সঙ্গে শিক্ষাও দিয়েছিল, যাতে করে পরে আমি আমার প্রথমের মনস্থির পরিবর্তন করি।
কুড়ি বছর বয়সে আমি বুঝতে পারি যে ট্রেড ইউনিয়ান যেমন কর্মচারীদের দাবি এবং উন্নত জীবন ধারনের জন্য শক্তিশালী হাতিয়ার, অন্যদিকে তেমনি এ ট্রেড ইউনিয়ন রাজনৈতিক দলগুলোর শ্রেণী সংগ্রাম করারও যন্ত্র।
সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা ট্রেড ইউনিয়ান চরিত্রের এ দিকটা ভালভাবেই বুঝত এবং তা প্রয়োজনে নিপুণভাবে ব্যবহার করত। তারা ট্রেড ইউনিয়ান নামক যন্ত্রটিকে এমন নিপুণভাবে ব্যবহার করত যে তাতে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। অপরদিকে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ট্রেড ইউনিয়ানের চরিত্রের এ দিকটা অক্ষম হওয়ায় রাজনীতির পটভুমিকা থেকে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে। তারা সব সময় ভেবে এসেছে যে তাদের একগুয়েমী এ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের বৃদ্ধি বন্ধ করবে এবং রাজনৈতিক পটভূমিকা থেকে জায়গা হারিয়ে ফেলবে। কিন্তু এটা কখনই সম্ভব বা সত্যি নয় যে ট্রেড ইউনিয়ান মুভমেন্ট জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থি। সত্যি বলতে কি এর উল্টোটাই হল অনেক বেশি সত্য। যদি ট্রেড ইউনিয়ানের কার্যকলাপ শ্রেণী উন্নতির কাজে লাগান যায় এবং তা সাফল্যের সঙ্গে করা যায় তবে সেই ট্রেড ইউনিয়ান মুভমেন্ট পিতৃভূমি এবং শাসককুলের বিরুদ্ধে তো যাবেই না, বরং জাতির সত্যিকারের উন্নতির সহায়ক হবে। এ পথে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন হল জাতির শিক্ষায় একটা অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গবিশেষ। এটাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নেওয়া উচিত, কারণ এটা শুধু সামাজিক দূষিত বীজাণুগুলিকে মারবে না বরং জাতির পারিপর্শ্বিক এবং সামগ্রিক উন্নতির পথে জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।
সুতরাং ট্রেড ইউনিয়ান যে অতি প্রয়োজনীয় এটা জিজ্ঞাসা করা শুধু নিম্প্রয়োজন তা নয়, অবাঞ্ছনীয়ও বটে।
যতদিন পর্যন্ত কর্মচারীরা সামাজিক সচেতন না হয় এবং ন্যায্য বিচার সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করে, ততদিন পর্যন্ত তাদের মালিকদের কর্তব্য, যারা আমাদের জনসাধারণের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশও বটে, সাধারণ ব্যক্তিদের লোভ এবং অযৌক্তিক স্বার্থ থেকে তাদের রক্ষা করা। জাতীয় স্বার্থেই কেবল যেমন জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাস এবং আস্থা রাখা উচিত নয়, সুস্বাস্থ্যের জন্য এটা প্রয়োননীয়ও বটে।
এ দুই ব্যবস্থাকে অসাধু মালিকেরা ভয় দেখিয়ে দাবিয়ে রেখে জাতির একজন সদস্য হিসেবে চরম অন্যায় করে চলত। তাদের ব্যক্তিগত তীব্র লালসা এবং দায়িত্বহীনতাই ভবিষ্যতের যত গণ্ডগোলের বীজ বপন করেছিল। এ অন্যায়গুলোর প্রতিরোধ করা মানেই দেশের উন্নতি করা।
এখানে বলা নিষ্প্রয়োজন যে যদি কোন শ্রমিক মালিকের তরফ থেকে অন্যায়ভাবে বঞ্চিত হয়, তবে তার পরিপূর্ণ অধিকার আছে সেকথা স্বাধীনভাবে চিন্তা করার অথবা সে চাকরিস্থল পরিত্যাগ করার। না, এ যুক্তি বর্তমানে যে প্রসঙ্গ আলোচনা করতে বসেছি তা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাবে। এ সামাজিক বিক্ষোভ দূরে সরানো উচিত কিনা এটাই হল আমাদের কাছে বড় প্রশ্ন। যদি উচিত হয় তবে এমন এক শক্তিশালী অস্ত্র দিয়ে সংগ্রাম করতে হবে যাতে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে একজন শ্রমিকের পক্ষে তার মালিকের প্রচণ্ড ক্ষমতার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। এটাই যদি চলার আদর্শ হত, তবে তো সংঘর্ষের কোন কারণই থাকত না। এখানে প্রশ্ন হল কে বেশি শক্তিশালী? যদি ব্যাপারটা অন্যরকম হত বিচারের মানবত্ব ঝগড়াটাকে সম্মানের সঙ্গে মিটিয়ে দিতে পারত; অথবা ব্যাপারটাকে আরো বেশি সঠিকভাবে উপস্থাপনা করা যেত যাতে ঝগড়াটা গড়াতেই পারত না।
যদি অসামাজিক বা ঘৃণামিশ্রিত ব্যবহার মানুষকে প্রতিরোধ করতে বাধ্য করে, তখন শক্তিশালী প্রতিপক্ষ তাদের নিজস্ব মতবাদ সেই প্রতিরোধের ওপরে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, আইনসভা আইনের সাহায্যে এসব শয়তানী মতবাদগুলোকে অবশ্যই দূরীভূত না করলে। সুতরাং এর থেকে বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে একক শ্রমিককে যদি এ যুদ্ধে জিততে হয় তবে তাকে তার সহকর্মীদের নিয়ে একটা যুজফ্রন্ট তৈরি করে তবে মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে সগ্রামে নামতে হবে। অবশ্য মালিক তার পেটোয়া লোকদের জড়ো করার আগেই। কারণ মালিক সবসময় তার পেটোয়া লোকগুলোকে জড়ো করে নিয়েই শিল্প অথবা বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা করে থাকে।
এভাবেই শুধু যে ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ করতে পারে তা নয়। ভবিষ্যতের বাস্তব ফলাফলের রাস্তাও খুলে দিতে সক্ষম হয়। এ পথেই তারা তাদের সংঘর্ষের কারণগুলো দূর করতে পারে; যেগুলো হল তাদের অসন্তোষের মূল কারণ।
ট্রেড ইউনিয়ান যে সত্যিকারের পথে কাজ করে না তার জন্য দায়ী হল যারা আইনের সাহায্যে সংস্কারের বা সংস্কার করা হলেও সেগুলোকে পেছন থেকে ছুরি মেরে বাস্তবে রূপায়িত হতে দেয় না। আর এ সবগুলোই তারা করে তাদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি দিয়ে।
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক সচেতনতা ছিল না এসব বোঝার বা ইচ্ছে করেই বুঝতে চাইত না যে ট্রেড ইউনিয়ান মুভমেন্ট কত দরকারি। আর সেই সুযোগে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট্রা ফায়দা উঠিয়েছে; পুরো মুভমেন্টটাকেই নিজেদের দিকে টেনে নিয়েছে। এভাবে শক্ত একটা দুর্গ বানিয়ে যখনই সংগ্রাম আকার ধারণ করেছে তার আড়ালে মুখ লুকিয়েছে; সংগ্রামের সত্যিকারের উদ্দেশ্যে মানুষ বিস্মৃত হয়ে গেছে তার বদলে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এসে জায়গা দখল করে বসেছে। ট্রেড ইউনিয়ান মুভমেন্ট যে উদ্দেশ্য নিয়ে শুরু হয়েছিল তা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের বিপদে ফেলতে সমর্থ হয়নি। বরং তারা সংগ্রামটার গতি রুদ্ধ এবং বিপথগামী করে দিয়েছে নিজেদের সুবিধার জন্য।
কয়েক যুগের মধ্যেই সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা নিপুণ হাতে ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্টটাকে যেটা সৃষ্টি হয়েছিল মানবাধিকার রক্ষার জন্য, সেটাকে জাতীয় অর্থনীতির ধ্বংস যন্ত্রে পরিণত করে, শ্রমিকদের স্বার্থ যাতে এক মুহূর্তের জন্যও তাদের উদ্দেশ্যের পথ রোধ করতে না পারে। কারণ রাজনীতিতে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা খুব একটা কঠিন কাজ কিছু নয়; যদি একপক্ষ যথেষ্ট অসৎ আর অপরপক্ষ প্রচণ্ডরকমের নিষ্ক্রিয় ও অনুগত হয়। এ ব্যাপারে দেশের বর্তমান অবস্থা ওপরের দুটো পথকেই মেনে নিয়েছিল।
এ শতাব্দীর প্রারম্ভে ট্রেড ইউনিয়ান মুভমেন্ট তার নিজস্ব অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে এটার সৃষ্টি তা হারিয়ে ফেলেছিল। সময়ের স্রোতে এ ট্রেড ইউনিয়ান মুভমেন্ট সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের রাজনৈতিক ছায়ায় চলে যায়; শেষ পর্যন্ত একটা শ্রেণী সংগ্রামের ব্যাপারে প্রাচীনকালে অবরুদ্ধ নগরীর দেওয়াল ভাঙার জন্য কাঠের গুঁড়ির মুখে যে লোহা বাঁধানো থাকত, এ ট্রেড ইউনিয়ান সেই লোহা বাঁধানোর পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়। ওদের পুরো পরিকল্পনা ছিল অর্থনৈতিক রাজপ্রাসাদকে, যেটা অতি কষ্টে দিনের পর দিন বহু পরিশ্রমে গড়ে তোলা হয়েছিল; আঘাতের পর আঘাতে সেটাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া। একবার এ উদ্দেশ্য সফল করতে পারলে সমগ্র দেশের ধ্বংস শুধু সময় অপেক্ষার ব্যাপার, কারণ তার আগেই তো দেশ অর্থনৈতিক বুনিয়াদ থেকে বঞ্চিত। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা কখনই শ্রমিকদের স্বার্থ দেখেনি। এবং দিনে দিনে এটা শূন্যের দিকে এগিয়ে চলে যতক্ষণ না পর্যন্ত ধূর্ত নেতারা উপলব্ধী করে জনতার সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক চিন্তাধারা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থে উপেক্ষা করা উচিত; কারণ যদি জনতার মধ্যে একবার আত্মসন্তুষ্টির ভাব আসে তা হলে আর কখনই এ রাজনৈতিক সংগ্রামে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবে না।
শ্ৰেণী সগ্রামের এ বিভিন্ন ভবিষ্যত, তাদের এত বেশি উদ্বিগ্ন করে তোলে যে জনতার অসন্তোষ ভবিষ্যতে হয়ত বা আর অস্ত্র হিসেবে কাজ করবে না; এ ভেবে সমাজ সংস্কারের প্রাথমিক ধাপগুলো তারা শুধু প্রতিরোধই করে না, ভেঙেও দেয়। দেশের অবস্থা তখন এমনই শোচনীয় যে এ সব নেতাদের বে-আইনি কাজ করার জন্য কোনরকম অসুবিধে হয় না।
যেহেতু জনতাকে সবসময় তাদের দাবি কি করে বাড়াতে হয় সেটাই দেখানো হত, তাই তাদের সন্তুষ্টির ভাব এমন দিশেহারা হয়ে যায় যে যেরকম উন্নতির ব্যবস্থাই করা হোক না কেন, তাদের কাছে তার কোন মূল্যই থাকে না। সুতরাং এটা তখন শ্রমিক শ্ৰেণীকে বোঝানো অসম্ভব ছিল না যে এ ধরনের হাস্যাস্পদ ব্যবস্থা হল তাদের সংগ্রাম শক্তিকে ভেঙে দেওয়ার পৈশাচিক পথ; শুধু তাই নয় তাদের সংগ্রামের ক্ষমতাও ভেঙে দেওয়া এর উদ্দেশ্য। যাদের বোঝবার ক্ষমতা আছে যে সাধারণ মানুষের চিন্তাশক্তি কতটুকু, তারা এ পথের সাফল্যে আশ্চর্য হবে না।
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের এ কলাকৌশলগুলোর প্রতি বরাবরই এক ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধ ছিল। কিন্তু তাদের তরফ থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করার জন্য কোন সংগঠন করারই চেষ্টা করা হয়নি। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিকদের বরাবরই একটা ভয় ছিল যে শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা ভাল হলেই বুর্জুয়া সম্প্রদায়ে যোগ দেবে; সুতরাং সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের হাত থেকে শ্রেণী সংগ্রামে সবচেয়ে বড় অস্ত্রটাই হাতছাড়া হয়ে যাবে। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটেনি।
বিপক্ষদের আক্রমণ করার চেয়ে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় নিজেরাই ওদের চাপ এবং ভয় প্রদর্শন মেনে নিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত এ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় এমন একটা পথ বেছে নেয় যা এত মন্থর এবং ভোতা, ফলে অচিরে সেটাকে বর্জন করতে বাধ্য হয়। সুতরাং সমস্ত অবস্থাটাই সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে যেখানে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ব্যাপারটাতে মাথা গলাবার পূর্বে ছিল; কিন্তু ততদিনে জনসাধারণের অসন্তোষ চরমে উঠেছে।
বিদ্যুৎ ঝড়ের মত মুক্ত ট্রেড ইউনিয়ান রাজনৈতিক দিগন্তে এবং ব্যক্তিগত জীবনের ওপর চক্র কেটে বেড়ায়। জাতীয় অর্থনীতির অনিশ্চয়তা এবং পরনির্ভরতা হল দেশের এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে এক চরম বিপজ্জনক ব্যাপার। সর্বোপরি এ মুক্ত ট্রেড ইউনিয়ান গণতন্ত্রকে শুধু হাস্যাস্পদ করে তোলেনি, ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়াও বাঁধিয়ে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতাকে কলংকিত করে ধ্বনি তুলেছে— তোমরা যদি আমাদের সঙ্গে হাত না মিলাও আমরা তোমাদের মস্তিষ্ক চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেব।
সেই সময়ে আমি মানবত্বের সত্যিকারের বন্ধুকে চিনতে পারি। দিনে দিনে আমার জ্ঞান যেমন বিস্তৃত হয়, তেমনি গভীরতাও বাড়ে; তবু অন্তত এ বিষয়ে আমার মত পরিবর্তনের কোন কারণ খুঁজে পাই না।
যতই সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির বাইরের রূপের সঙ্গে পরিচিত হই, তত বেশি এ মতবাদটার অন্তর প্রকৃতি দেখার জন্য আমার তৃষ্ণা বেড়ে ওঠে।
এ তৃষ্ণা নিবারণের উপায় পার্টির প্রচার পুত্রের মাধ্যমে ছিল না। কারণ ওদের অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলোর সঙ্গে যে বিবৃতি থাকত তা মিথ্যা এবং অগভীর। ওদের রাজনৈতিক লক্ষ্য বলতে কিছু ছিল না। উপরন্তু যুক্তিতর্ক উপস্থাপনায় ওরা যে আধুনিক ছল চাতুরীর আশ্রয় নিত তা ছিল আমার কাছে চরম অপ্রীতিকর। ওদের বড় বড় কথা শুধু শূন্যগর্ভ এবং ধারণাতীত বাক্যে ভরা। হঠাৎ পড়লে মনে হয় এগুলো মহৎ চিন্তার ফসল; কিন্তু এগুলো ছিল সত্যিকারের চিন্তা-শূন্যতায় ভরা এবং অনর্থক কতগুলো শব্দের সমষ্টি। আজকের এ আধুনিক সমাজে যে কোন লোক নিজেকে ক্ষয়িত বলে মনে করে, কারণ এ শহরে জীবনের বিচিত্র গোলকধাঁধা তাদের মনকে বিপথগামী করে তোলে। সেজন্য হয়ত বা এ দুর্গন্ধময় ধোঁয়ার মধ্যে সে তার স্বাধীনতার নামে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার গন্ধ পায়। এ লেখকগুলো আমাদের জনগণের এক অংশের যে সুবিদিত লাঞ্ছনা সেইগুলোকে শুধু দেখে; আর তা দেখেই বিশ্বাস করে যে ব্যক্তিকে ধারণায় আনা যায় না, সে নিশ্চয়ই অত্যন্ত জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান।
এ মতবাদের তত্ত্বের দিক দিয়ে মিথ্যা উক্তি এবং অবাস্তবতা, এর বাইরের অভিব্যক্তির মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। আমি ক্রমে ক্রমে এর শেষ লক্ষ্য কি সেটা পরিষ্কার বুঝতে পারি।
এ মুহূর্তগুলোতে আমি সেই ভবিষ্যতের অন্ধকার প্রতিচ্ছবি এবং অমঙ্গলের পূর্বাভাস যেন দেখতে পাই। আমার যে শিক্ষা, সেই শিক্ষার ইন্ধন জুগিয়েছে অহমিকা আর ঘৃণা যেটা গাণিতিক ছকে ফেলে হিসেব করলে সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সে সাফল্য হবে মানবত্বের ওপরে প্রচণ্ড এক মুষ্ঠাঘাত।
ইতিমধ্যে এ ধ্বংসমূলক শিক্ষা এবং সত্যিকারের জনসাধারণের চরিত্র, যেটা এতদিন পর্যন্ত আমার কাছে অজ্ঞাত ছিল স্পষ্ট বুঝতে পারি।
ইহুদীদের সম্পর্কে অজ্ঞানতা হল সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির প্রকৃত চরিত্র এবং সত্যিকারের লক্ষ্য বোঝার চাবিকাঠি। যে লোক এ জাতটার সম্পর্কে তার দৃষ্টির সামনের কুয়াশা সরিয়ে দিতে পেরেছে, তার পক্ষে এ পার্টির অর্থ এবং লক্ষ্য পরিষ্কারভাবে বোঝা সম্ভব; এবং তারপর এ অন্ধকার তথাকথিত সামাজিক উন্নতির কুয়াশা সরিয়ে সে মার্কসীয় মতবাদের নিকট আসল রূপ দেখতে পারে।
আজকে আমার পক্ষে বলা অত্যন্ত কষ্টকর, প্রায় অসম্ভব যে কখন ‘ইহুদী’ শব্দটা আমার মনে বিশেষ এক চিন্তাধারার উদয় করেছিল। আমি ঠিক স্মরণে আনতে পারি না, পিতার জীবিতকালে বাড়িতে থাকাকালীন এ শব্দটা আমি শুনেছি কিনা। যদি এ শব্দটা কোন অপমানকর ভাষায় ব্যবহার করা হত তাহলে সেই বৃদ্ধ লোকটি ভাবত যে এটা একমাত্র অশিক্ষার ফল। কারণ তার চাকরি জীবনে এত বেশি এবং বিভিন্ন ধরনের লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করেছে যে তাকে জাতীয় সংস্কারমুক্ত বলা চলে। যদিও তার জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত প্রখর ছিল, এবং তার সেই প্রভাব আমার ওপরেও ভালভাবে বর্তেছিল। স্কুল জীবনেও আমি আমার এ ধারণার পরিবর্তনের কোন কারণ খুঁজে পাইনি; যেটা আমার মনের মধ্যে বাড়িতে থাকাকালীন বেড়ে উঠেছিল।
মাধ্যমিক স্কুলে আমার সাথে একটা ইহুদী ছেলে পড়াশুনা করত যার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালই ছিল। কিন্তু তার মৌন ভাব এবং কয়েকটা ব্যাপারে আমরা সর্বদা সতর্ক থাকতাম। এছাড়া আমি এবং আমার বন্ধুদের ওর সম্পর্কে অন্য কোন রকম ধারণা ছিল না।
চৌদ্দ পনের বছর বয়সে আমি ‘ইহুদী’ শব্দটার সঙ্গে পরিচিত হই রাজনৈতিক প্রতিবেদনের সম্পর্কে। এসময়ে আমার মনে ইহুদী সম্পর্কে একটা বিরূপ ভাব জাগে। সত্যি বলতে কি মনের এ অবস্থা আমি সব সময়ে আয়ত্তে রাখতে পারিনি। বিশেষ করে ধর্মের সম্পর্কে সংঘর্ষের ব্যাপারগুলোতে। কিন্তু এছাড়া ইহুদীদের সম্পর্কে অন্য কোন বিরূপ ধারণা আমার মনে সে সময় ছিল না।
লিনৎস শহরে ইহুদীদের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল। শতাব্দী ধরে এসব ইহুদী সেখানে বসবাস করার ফলে বাইরে থেকে দেখতে ইউরোপের আর পাঁচজন অধিবাসীর মতই লাগত এবং বলতে দ্বিধা নেই আমি অন্যান্যদের মত তাদেরও জার্মান বলেই ভাবতাম। এর কারণ হল মানুষ হিসেবে তাদের বাইরের চেহারায় অন্য কোন পার্থক্য খুঁজে পাইনি। একমাত্র ধর্মীয় ব্যাপারগুলোয় তাদের অদ্ভুত আচরণ ছাড়া। আমার তখন ধারণা ছিল যে তাদের ধর্ম-বিশ্বাসের জন্য অন্যেরা তাদের ওপর নির্যাতন চালায় এবং আমারও তাদের প্রতি তীব্র একটা ঘৃণা বোধ জেগে ওঠে। তখন পর্যন্ত আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না যে ইহুদীদের সম্পর্কে একটা বিদ্বেষের ভাব দেশ জুড়ে ফলু ধারার মত চলে আসছে। এরপরে আমি ভিয়েনায় চলে আসি।
জনসাধারণের চিন্তাধারায় আমি বিভ্রান্ত হই যখন আমি স্থাপত্যকর্মে নিযুক্ত। তখন অবশ্য নিজের বিপদের জন্যও আমি হতাশাগ্রস্ত। প্রথমে বুঝতে পারিনি সে শহুরে জনজীবন কতগুলো বিভিন্ন সামাজিক স্তরে গঠিত। যদিও তখন ভিয়েনার অধিবাসীর সংখ্যা কুড়ি লক্ষ, কিন্তু ইহুদীদের সংখ্যা মাত্র লাখ দুয়েক। সেই জন্যই ব্যাপারটা আমার নজরে আসেনি। সেই প্রবাস জীবনে প্রথম কয়েক সপ্তাহ আমার মনে এবং চোখে নতুন ধারণা ও চিন্তাধারার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেনি। যখন আমি ধীরে ধীরে আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিলাম, তখন চোখের সামনে এ গোলমেলে ছবিগুলো এক এক করে আমার সামনে পরিষ্কার হয়ে গেল; আমি আমার নতুন জগতটা সম্পর্কে অবিসাংবাদিত ধারণা নিতে সক্ষম হই ও ইহুদী সমস্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই।
আমি বলতে চাই না যে প্রথমে আমি যেভাবে এ সমস্যাটার সঙ্গে পরিচিত হই, তা খুব একটা অপ্রীতিকর ছিল। ইহুদীদের সম্পর্কে তখন আমার ধারণা যে ওরা অন্যধর্মী, সুতরাং মানবত্বের খাতিরে অন্যধর্মী বলে তাদের আক্রমণ করার বিপক্ষে আমি ছিলাম। এবং ইহুদী বিরুদ্ধ যে সংবাদপত্রগুলো ভিয়েনাতে প্রচলিত ছিল তাদের সংস্কৃতির প্রতি আমার সন্দেহ ছিল। মধ্যযুগে যে বিশেষ কতগুলো ঘটনা ঘটে গিয়েছিল সেগুলোও আমার স্মৃতিতে ছিল এবং আমি চাইতাম যে এগুলোর পুনরাবৃত্তি আর যেন না হয়। বিশেষ করে বলতে গেলে এ ইহুদী বিরুদ্ধ পত্রিকাগুলো মোটেই প্রথম শ্রেণীর ছিল না। কিন্তু আমি তখন এর কারণটা বুঝতে পারিনি এবং ভেবেছি ঈর্ষার ফল, যার মধ্যে এতটুকুও সপ্রচেষ্টা নেই।
আমার নিজস্ব অভিমত আমি গাম্ভীর্যের সঙ্গে পর্যালোচনা করতেই অভ্যস্ত ছিলাম; যে কারণে প্রথম শ্রেণীর সংবাদপত্রগুলো হয় তার উত্তর দিত, নয় সেগুলো পাশ কাটিয়ে যেত। ভবিষ্যতে আমি বুঝতে পেরেছি যে এটাই হল সবচেয়ে সম্মানজনক পথ।
যে পত্রিকাগুলোকে পৃথিবীর মুখপাত্র বলা হয়, যেমন নয়ি প্রেসে, ভিনার টাগেরাটে ইত্যাদি পড়তাম। আশ্চর্য হয়ে যেতাম এরা কত বেশি পরিমাণে এদের পাঠকদের জন্য সংবাদ পরিবেশনা করে। তার চেয়ে বড় কথা কোন একটা বিশেষ সমস্যাকে এরা নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে বিচার করে থাকে। তাদের অভিজাত ভঙ্গিতে লেখা আমার ভাল লাগত। তবে কখনো কখনো এ প্রচণ্ড রকমের স্টাইল সর্বস্ব সাংবাদিকতা আমার পছন্দ হত না। কিন্তু সারা পৃথিবীর প্রধান প্রধান শহরগুলোর সংবাদ রাখতে আমি ভালবাসতাম।
আমার ধারণায় ভিয়েনাও পৃথিবীর প্রধান নগরীগুলোর অন্যতম; সে কারণেই ভিয়েনার সংবাদের স্বল্পতা সম্পর্কে কোন নালিশ করা চলে না। কিন্তু ভিয়েনা প্রেসের রাজবংশীয়দের প্রতি এ চাকরের মত আনুগত্য আমাকে বিরক্ত করত। যদি হাববুর্গের প্রতি কোন আক্রমণ করা হত, সেটা যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে পাঠকদের কাছে হাজির করা হত না। এটা পৃথিবীর অন্যতম চালাক একজন রাজার প্রতি প্রচেষ্টা, তখন গৌরবের সঙ্গে তুলে না ধরাটা আমি বোকামী বলেই মনে করতাম। এগুলো যেন আমাকে স্মরণ করিয়ে দিত বনমোরগ তার সঙ্গিনীকে চিন্তার সমুদ্রে ডুবিয়ে দিয়ে হঠাৎ পালিয়েছে। আমি ভাবতাম এ চালাকি আর কিছুই নয়, ঢিলে গণতন্ত্রের আদর্শের ওপর রঙ করা মতবাদ মাত্র। এটা হল কতগুলো অপদার্থ লোকের আনুকূল্য কুড়াবার অপচেষ্টা। আমি ব্যক্তিগতভাবে ভাবতাম এ ধরনের সংবাদ ভিয়েনার সংবাদপত্রগুলোর সুনামের কলঙ্ক বিশেষ।
ভিয়েনায় থাকাকালীন রাজনীতি বা সংস্কৃতি যে কোন ব্যাপারেই হোক জার্মানিতে যা ঘটত তার প্রতি নজর রাখতাম। এবং বলতে আপত্তি নেই নিজেকে গর্বিত মনে হত যখন ভাবতাম কী ভাবে অস্ট্রীয়াকে অস্বীকার করে নতুন সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হল। সে সাম্রাজ্যের বৈদেশিক নীতি রীতিমত প্রশংসার যোগ্য, যদিও আভ্যন্তরিক নীতি ততটা নয়। বিশেষ করে দ্বিতীয় উইলহেলমের বিরুদ্ধে প্রচারটাকে কোন মতেই আমি মেনে নিতে পারিনি। কারণ আমার চোখে দ্বিতীয় উইলহেলম্ শুধু একজন জার্মান সাম্রাজ্যের অধীশ্বরই নন, জার্মান নৌ-বাহিনীরও স্রষ্টা। বিশেষ করে রাইখষ্টাগে তাকে বক্তৃতা দিতে না দেওয়ায় আমি ক্রুদ্ধ হই। কারণ যারা তাকে বক্তৃতা দিতে দেয় না তাদের সে ক্ষমতাই নেই। পার্লামেন্টের এক অধিবেশনে তথাকথিত রাজহংসগুলো অনেক বেশি প্যাক প্যাক করে যা পুরো রাজবংশীয়দের এমন কি দুর্বলতম রাজার সময়েও পুরো শতাব্দী ধরে এর চেয়ে অনেক কম কাজ হয়েছে।
যখন ভাবি একটা ব্যক্তির মধ্যে আধা বুদ্ধিসম্পন্ন কোন জাতির বিধানকর্তা হিসেবে রাইখষ্টাগের সমালোচনা করার অধিকার রাখে ও জনতাকে লেলিয়ে দেয় এবং তার দ্বারা রাজমুকুটকে কঠোর ভৎসনা জনতার কাছ থেকে শুনতে হয়, তখন এসব নির্বোধ বিধান সভার সভ্যগুলোর ওপরে প্রচণ্ড রকমের রেগে যাই।
সবচেয়ে বিরক্তিকর যখন দেখি ভিয়েনা প্রেস রোজই গিরগিটির মত ভোল পাল্টায়। হাসবুর্গ রাজপ্রাসাদের গাড়ি টানার ঘোড়াগুলোর লেজ ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে ভিয়েনা প্রেসেরও মত বদলায়। সাথে সাথে এ প্রেস ভিয়েনার জনতার মধ্যে জার্মান সাম্রাজ্য সম্পর্কেও একটা শত্রুতার আতংক জাগিয়ে তোলার প্রয়াস করে। কিন্তু আমার মতে সেই শক্রতা দৈন্যবেশে সাজানো। সঙ্গে সঙ্গে এও আবার জানায় যে জার্মানির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কোনরকম ইচ্ছেই নেই। ইশ্বরের দোহাই, তারা এরকম ভাণ করে যে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তারা বিশেষ বন্ধুরই কাজ করেছে। এবং দুই দেশের বন্ধুত্ব রক্ষার জন্য এটা হল সাংবাদিকসুলভ সততা; এ কথার আড়ালে তারা একটা বিষাক্ত ক্ষতে আঙুল দিয়ে খুঁচিয়ে আর বিষাক্ত করে তোলে।
এ ধরনের ব্যাপারগুলো আমার রক্তকে যেন টগবগিয়ে ফোঁটাচ্ছে।
একথা অস্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে এ বিষয়ে ইহুদী বিরোধী পত্রিকা দ্য ডয়েচে ভল্কসূব্ল্যাটের বক্তব্য অনেক বেশি পরিষ্কার এবং সুন্দর।
বড় বড় নামী পত্রিকাগুলো যেভাবে ফ্রান্সের জয়গানে মুখর, ভাবলেও আমার শিরায় শিরায় রক্ত চলাচল দ্রুত হয়ে ওঠে। একজন জার্মান হিসেবে তথাকথিত মহৎ সংস্কৃতি সম্পন্ন একটা জাতির শ্রুতিমধুর জয়গানে লজ্জায় মাথা নিচু হয়ে যায়। এ নষ্টামী ভরা জয়গানের জন্যই একাধিক বার এ বিখ্যাত পত্রিকাগুলো আমি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। সেই কারণেই আমি বর্তমানে একমাত্র ভল্টকব্লাটের পত্রিকাটা পড়ি। মাপে ছোট হলেও এসব বিষয়ে পত্রিকাটার লেখা বেশ পরিচ্ছন্ন। যদিও ওদের চড়া ইহুদী বিদ্বেষী সুর আমার মনের সঙ্গে মিলত না; তবু ওদের যুক্তি আমাকে বারে বারে ভাবিয়ে তুলত।
যাহোক, এসব পড়াশোনার জন্যই আমি ভিয়েনার সেই বিশেষ মানুষটা, সংগ্রামটাকে, এবং ভিয়েনার ভবিষ্যত বুঝতে পারি। মানুষটা হল ডক্টর কার্ল লয়েগার আর তার সংগ্রামের নাম হল ক্রিশ্চান সোশ্যালিস্ট মুভমেন্ট। যখন প্রথম ভিয়েনায় আসি, তখন কিন্তু উভয়েরই বিরোধিতা করেছিলাম। মানুষটা এবং তার সংগ্রাম সম্পর্কে আমার ধারণা ছিল–এরা উভয়েই প্রতিক্রিয়াশীল।
এমন কি ডক্টর লয়েগার এবং তার কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করার পরেই আমার অভিমত আমি বদলে ফেলি। ধীরে ধীরে সেটা প্রশংসায় রূপান্তরিত হয়; কারণ তখন আমি বিচার করতে সক্ষম। শুধু সেদিনই নয়, আজকে পর্যন্ত আমি ডক্টর কার্ল লয়েগারকে শ্রেষ্ঠ জার্মান মেয়র বা নগরপালের সঙ্গে তুলনা করি। এবং ক্রিশ্চান সোশ্যালিস্ট মুভমেন্টের প্রতি আমার এ মানসিক পরিবর্তন আমাকে অনেক কুসংস্কারকে ঝেড়ে ফেলে দিতে সাহায্য করেছে।
আমার ইহুদী বিদ্বেষী মনোভাবের পরিবর্তন হয়, তবে সহজে নয়। বরং কষ্ট করেই এ মতবাদের পরিবর্তন করতে হয় আমাকে। সত্যি বলতে কি তার জন্য আমাকে মানসিক অনেক সংঘাত সহ্য করতে হয়েছে। এবং এ সংঘর্ষ হল ভাবালুতার সঙ্গে বাস্তবতার। শেষ পর্যন্ত বাস্তবই জয়ী হয়েছে সেই মানসিক টানাপোড়েনের সংঘাতে।
বছর দুই বাস্তবতার কাছে ভাবালুতা ছিন্নভিন্ন হয়ে পলায়ন করে এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গিই অভিভাবক ও আমার মনোজগতের পরিচালক হয়ে বসে।
সেই তিক্ত মানসিক সংঘর্ষের দিনগুলোতে যখন ভাবালুতার আর বাস্তবতার টানাপোড়েনিতে দিনগুলো পাড়ি দিচ্ছি, তখন ভিয়েনার রাস্তায় প্রত্যক্ষ কতগুলো শিক্ষা আমার আমূল পরিবর্তনে সাহায্য করে। এমন একটা সময় আসে যখন আমি আর আগের মত অন্ধের ন্যায় রাস্তাঘাটে চলাফেরা করি না; বরং চোখ কান এমনভাবে খুলে রাখি যাতে শুধু বাড়িঘরই নয়, মানুষগুলোকেও পর্যবেক্ষণ করতে পারি।
একদিন শহরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, আজানুলম্বিত কালো রঙের কোট পরা একজনের মুখোমুখি হই, প্রথমেই ভাবি : এ কি একজন ইহুদী? কিন্তু লিনৎসে তো এ ধরনের চেহারা আগে দেখিনি। আমি গোপনে সতর্কতার সঙ্গে লোকটাকে পর্যবেক্ষণ করি। সেই বিদেশী চেহারাটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় মনে হয় এ জার্মান নয় তো?
আমার বরাবরের অভ্যাসের মত আমি এর সমাধানে বইপত্র হাতড়াতে শুরু করি। এ প্রথম জীবনে অনেক কটা পয়সার বিনিময়ে ইহুদী বিদ্বেষী প্রচারপত্রও কিনে ফেলি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রচারপত্রগুলোয় কিছুই পাইনি। কারণ এগুলো লেখা হয়েছে এভাবে–যে পাঠকদের ইহুদী সম্পর্কে জ্ঞান আগে থেকেই রয়েছে বা ইহুদীদের সঙ্গে এরা বিশেষভাবে পরিচিত। উপরন্তু প্রচারপত্রগুলোর ঢংটাই এরকম যে সেগুলো শুধু ভাসা ভাসা তাই নয়; অবৈজ্ঞানিক মতবাদেও ভর্তি। কয়েকটা সপ্তাহ এবং মাসের পর আমি আমার পুরনো চিন্তার রাজ্যে ফিরে আসি। কিন্তু বিষয়বস্তুটা এত বিস্তৃত এবং পরস্পর বিরোধী যে আবার মনে দ্বিধা আসে হয়ত বা বিষয়বস্তুটার প্রতি সঠিক মর্যাদা দেওয়া হবে না।
স্বভাবতই জার্মানদের কথা নয়, যারা হয়ত বা অন্য ধর্মের, কিন্তু ওরা হল সম্পূর্ণ অন্য জাতের এবং ধাতের লোক। যখনই আমি ইহুদীদের সম্পর্কে আরো বেশি খোঁজখবর নিয়ে ওদের পর্যবেক্ষণ শুরু করি, পুরো ভিয়েনাটা যেন আমার চোখের সামনে অন্য আলোতে ধরা দেয়। যত দেখি তত যেন তারা সাধারণ নাগরিকের থেকে আলাদা হওয়ায় আমার মনকে আকর্ষণ করে। বিশেষ করে শহরের অভ্যন্তর ভাগ এবং দানিয়ুব ক্যানেলের উত্তর দিকটা এ পতঙ্গের পালে অধ্যুষিত, যাদের সঙ্গে জার্মানদের বিন্দুমাত্র মিল নেই।
কিন্তু তবু আমার মনের মধ্যে যেটুকু দ্বিধার ভাব ছিল, ইহুদীদের একটা দলের কার্যকলাপে সে দ্বিধাটুকুও অল্প কয়েকদিনের মধ্যে উবে যায়। জিয়ানিজ নামে একটা বড় ধরনের বিপ্লব ওদের মধ্যে শুরু হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল জুডাইজম বা ইহুদী ধর্ম সম্পর্কে পরিষ্কার বক্তব্য রাখা; এবং ভিয়েনার শাসককুলের কাছে নিজেদের বক্তব্য জোরদার করে তুলে ধরা।
বাইরে থেকে হঠাৎ মনে হবে যে ইহুদীদের একটা দলই বোধহয় এ সগ্রাম এগিয়ে নিয়ে চলেছে, অপরদিকে বেশিরভাগ ইহুদীই এর বিপক্ষে, তাই একে বর্জন করেছে। কিন্তু অত্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে বুঝতে পারি যে এ আচরণ পুরো ব্যাপারটাকেই ধোঁকা দেবার জন্য। এবং তা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। তার ওপর তত্ত্বটাকে এমনভাবে রূপ দেওয়া হয়েছে, যার প্রয়োজন ছিল। সম্ভবত সমস্ত ব্যাপারটা থেকেই সাধারণ জনমানসকে প্রতারণা করার জন্য। ইহুদীদের যে অংশটা নিজেদের উদারতা দেখিয়ে জিয়োনিস্টদের সংগ্রামে অংশ নিত না, কিন্তু ভাই হিসেবে তারা প্রকাশ্যে তাদের সমর্থন করত। সত্যি বলতে কি নিজেদের ধর্মের ওরা তাতে ক্ষতিই বেশি করত।
তাদের পারস্পরিক বোঝাপড়ায় নিজেদের মধ্যে কোন দ্বন্দু ছিল না। উদার ইহুদী এবং জিয়োনিষ্টদের মধ্যে লোক দেখানো ওপর ওপর ঝগড়া আমাকে বিরক্ত করে তুলেছিল। কারণ এ ধরনের মনোবৃত্তি শুধু নৈতিক প্রবৃত্তিগুলোকেই নিচু করে না, একটা জাতির চরিত্রেও কলঙ্ক লেপন করে।
পরিষ্কার ও ছিমছাম, তা সে নৈতিক বা যে কোন বিষয়েই হোক, তার নিজস্ব একটা রূপ সাধারণ মানুষের কাছে আছে। যেটা জলের প্রতিবিম্বে মুখ দেখার মত। অবশ্য যদি তারা তা দেখে। ওদের পোশাক পরিচ্ছদে বিশ্রী গন্ধ আমাকে অসুস্থ করে তুলত। তাছাড়া ওদের এলোমেলো জামাকাপড় পরা দেখে নিচু স্তরের বিদেশী বলে মনে হত।
এ বিস্তারিত বর্ণনা কাররই ভাল লাগার কথা নয়; কিন্তু সত্যি কথাগুলোর মাধ্যমে একটা বিদেশী অপরিষ্কার জাতির সাংস্কৃতিক কয়েকটা দিকে কিছু ইহুদীর কার্যকলাপের রহস্যময়তা আমার কাছে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়। আমিও তার গভীরে প্রবেশ করি। এটা জীবনের সংস্কৃতির এমন একটা দিক যেখানে একটা ইহুদীও ছিল না যে তার নোংরা হাতের স্পর্শ রাখেনি। সেই ঘায়ের উপর ছুরি চালালেই যে কোন লোক মুহূর্তে আবিষ্কার করবে যে সেই পচনশীল দেহটায় পোকা কিলবিল করছে; আর হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে প্রায় সব ইহুদীই তখন অন্ধ।
আমার অভিযোগের পরিমাণও বাড়তে থাকে যখন দেখি সাংবাদিকতায়, সংস্কৃতিতে, সাহিত্যে আর নাটকে ওদের কার্যকলাপের বহর। উচ্চ নিনাদিত বিজ্ঞাপনগুলোয় খালি রঙচঙেরই মোড়ক। কেউ যদি সেই বিজ্ঞাপনগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে তবে দেখতে পাবে লেখক হিসেবে যার নাম বিশেষভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, সে একজন গোঁড়া ইহুদী। এভাবেই একটা সংক্রামক ব্যাধি ধীরে ধীরে জনসাধারণের ভেতরে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাচীনকালের কালো প্লেগের থেকেও এ রোগ অনেক বেশি তীব্র। বিশেষ করে যে ভীষণ পরিমাণে এতে বিষ মিশিয়ে জনসাধারণের কাছে পরিবেশন করা হত। স্বভাবতই যে লেখক যত নিচুমানের এবং চালক, তত বেশি তার জনপ্রিয়তা। এক এক সময় সেটার পরিমাণ এত বেশি হয়ে দাঁড়াত যে মনে হত কেউ যেন নর্দমার ময়লা জল পাম্পের সাহায্যে সমস্ত জাতির মুখে ছুঁড়ে দিচ্ছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, এ ধরনের নোংরা লোকের ঘাটতি ছিল না। একজন গ্যেটের সৃষ্টির পেছনে অন্তত দশ হাজার এ ধরনের লুণ্ঠনকারি প্রকৃতি নিজেই নিয়ে আসে, যারা হল ভয়াবহ বীজাণুবাহক এবং মানুষের আত্মাকে বিষাক্ত করাই যাদের প্রধান কাজ। যদিও কথাটা চিন্তা করতে গা শিউরে ওঠে, তবু তা অস্বীকার করা যায় না যে বেশিরভাগ ইহুদীদের কাজই ছিল এটা; এবং তারা পুরোপুরি এ নিচু কাজেই নিজেদের পরিপূর্ণভাবে নিয়োগ করেছিল। এজন্যই কি ওদের সমাজের ওপরের স্তরের লোক বলা যায়।
এ নোংরা লোকগুলো সম্পর্কে আমি আরো বেশি খোঁজখবর নিতে শুরু করি। ফলে আরো বেশি তীব্র ইহুদী বিদ্বেষ আমার ভেতরে ছড়িয়ে পড়ে। যদি আমার মনোবৃত্তি ওদের বিরুদ্ধে এক হাজার গুণ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে, তবে সেই বৃদ্ধি পাওয়ার কারণগুলো খুঁজে বের করতে আমি সমর্থ।
সত্যিকারের ব্যাপারটা হল দশ ভাগের নয় ভাগ অশ্লীল সাহিত্য, নোংরা শিল্প এবং নাটকে বেলেল্লাপনা যারা চুটিয়ে করছে, তারা সমগ্র জনসাধারণের এক অংশ-ও নয়, এটাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। যা সত্যি তাকে তো স্বীকার করে নিতেই হবে। এরপর মনের মধ্যে গেঁথে যাওয়া ভাবটা নিয়েই ওয়ার্ল্ড প্রেস খুঁটিয়ে পড়তে শুরু করি।
সংবাদপত্রটার ভেতরে যত বেশি ঢুকতে থাকি তত বেশি সংবাদপত্রটার সততা সম্পর্কে শ্রদ্ধা হারাই। নিজেরই আশ্চর্য লাগে কী করে এ অসৎ সাংবাদিকতার প্রতি এতদিন শ্রদ্ধা পোষণ করে এসেছি। ক্রমে ক্রমে সংবাদপত্রটির প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মে যায়; এদের পুরো ধ্যান-ধারণাটাই ভাসা ভাসা এবং অলীক। শুধু তাই নয় সত্য ঘটনাগুলোও এমনভাবে সাজানো যে তাতেই সত্যের থেকে মিথ্যাই বেশি পরিবেশিত। লেখকেরা হল,–ইহুদী।
হাজার হাজার ঘটনা যেগুলোয় আগে মনোযোগ দিয়েছি, এখন দেখি সেগুলোর কোন গুরুত্বই নেই। পুরো ব্যাপারটাই আমার সামনে অন্য আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, যার মর্মার্থ এর আগে আমি বুঝে উঠতে পারিনি।
সাংবাদিকতার এ উদারতা আমার চোখে অন্য আলোতে পুরো ব্যাপারটা ধরা দেয়। প্রতিপক্ষকে আক্রমণের জন্য ওরা গাম্ভীর্যপুর্ণ স্বর ব্যবহার করে,–কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে ওদের সম্পূর্ণ নীরবতায় আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি যে ওরা কত ধূর্ত এবং কী পরিমাণে ঘৃণ্যভাবে পাঠককে ঠকিয়ে চলেছে। সুন্দর সুন্দর প্রবন্ধের মাধ্যমে ইহুদী লেখকদের প্রশংসা এবং জার্মান লেখকদের প্রতি বিরূপ সমালোচনা যেন ওদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তার সঙ্গে দ্বিতীয় উইলহেলকে আলত খোঁচা মারাও ওদের বাঁধাধরা মৌলিক নীতি, যেমন অপরদিকে ফ্রান্সের সংস্কৃতি এবং সভ্যতাকে ক্রমাগত পিঠ চাপড়ানো। প্রবন্ধের বেশিরভাগ বিষয়বস্তুই বস্তাপচা ও বিকৃত যৌন প্রসঙ্গে ভর্তি। বিশেষ করে সংবাদ পরিবেশনের পুরো ভাষার ধাচটাই বিদেশী ঢঙে পরিবেশিত। মোদ্দা কথা, খোলাখুলি জার্মানদের নির্লজ্জভাবে নিচু করার অপচেষ্টা।
কোন্ স্বার্থে ভিয়েনা প্রেস এ নীতি নিয়েছিল? হঠাৎ কোন কারণ ছাড়াই কি? এর সদুত্তরগুলো খুঁজে বের করতে গিয়ে ক্রমেই আমার মন আরো বেশি সন্দিদ্ধ হয়ে পড়ে।
এমনকি সমাজের বুকে গণিকা বৃত্তিতেও ইহুদীরাই সবচেয়ে বড় অংশ নিয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপীয় যে কোন শহরের চেয়ে এ শহরে তা অনেক বেশি স্পষ্ট। তবে দক্ষিণ ফ্রান্সের কয়েকটা বন্দর শহর ছাড়া। লিওপোল্ডস্টাড় শহরে রাতের বেলা রাস্তায় চলাফেরা করাই মুস্কিল। রাস্তাঘাটের প্রতিটি বাঁকে হঠাৎ যে রঙ মাখা মুখের দেখা পাওয়া যায়— যুদ্ধের পূর্বে এ জনপদবধূদের সঙ্গে জার্মানদের পরিচয়ই ছিল না। শুধু জার্মান সৈন্যরা ওদের মুখোমুখি হত ইষ্টার্ন ফ্রন্টে।
এ সত্যটার প্রথম আবিষ্কারে আমার মেরুদণ্ড বেয়ে একটা ঠাণ্ডা হিম-শিতল স্রোত যেন ছুটে নামে; এ সেই ঠাণ্ডা মাথার গণ্ডারের চর্মধারী, নির্লজ্জ ইহুদীর দল যারা চরম ঘৃণ্য কৌশলে এ বিশাল শহরের তলানীদের বিদ্রোহের চেষ্টাকে অহরহ প্রতারণা করে চলেছে। এ সত্য আবিষ্কারের পর সেই প্রেতাত্মাগুলোর ওপর আমি জ্বলে উঠি।
এবার আর মনে কোন দ্বিধা থাকে না যে করেই হোক ইহুদীদের দ্বারা সুসংগঠিত সমস্যাগুলো:জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতেই হবে। না, একাজে কিছুতেই পেছ পা হলে চলবে না। কিন্তু ততদিনে শিখে গেছি জীবনের শিক্ষা সংস্কৃতি বলতে গেলে সবক্ষেত্রেই ওদের অভিব্যক্তির সত্যিকারের অর্থটা খুঁজে বার করা। এবং বুঝতে পারি ইহুদীরাই হল সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির তাবড় নেতা। এ সত্যটা চোখের সামনের পর্দাটা তুলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আমার ভেতরকার এতদিনের মানসিক দ্বন্দটারও পরিসমাপ্তি ঘটে।
আমি আমার সহকর্মিদের মধ্যে দেখতাম কত সহজে এবং অহরহ একই ব্যাপারে তারা তাদের মত পরিবর্তন করে। কখনো কখনো তাদের এ পরিবর্তন ঘটতে সময় লাগে কয়েকটা দিন। কখনো বা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাদের মতামত পরিবর্তিত হয়। বিশেষ করে একটা ব্যাপার তো আমার মাথাতে কিছুতেই ঢুকত না যে একজন ব্যক্তি একক হিসেবে যুক্তিতর্কের জাল সুন্দর বিস্তার করে; কিন্তু সেই ব্যক্তিই যখন জনতার মুখোমুখি হয়, পুরো বিষয়টাই সে গুলিয়ে ফেলে এলোমেলো করে দেয়। আর এ ব্যাপারটাই লোকটাকে হতাশার সমুদ্রে নিমজ্জিত করে। আমি ঘন্টার পর ঘন্টা যুক্তিতর্ক দিয়ে তাদের স্বমতে আনতে চেষ্টা করতাম। শেষে আমার সাফল্যে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়তাম। কিন্তু পরের দিনই দেখতাম পুরো ব্যাপারটাই ভস্মে ঘি ঢালা। এটা চিন্তা করলে দুঃখ পেতাম যে ব্যাপারটার ইতিমধ্যে পরিসমাপ্তি ঘটে গেছে। পেণ্ডুলামের দোদুল্যমান অবস্থার মত তারা তাদের আগেকার মতামতের পর্যায়ে ফিরে গেছে।
ওদের অবস্থাটা অবশ্য আমি বুঝতে পারতাম। ও ওদের ভাগ্যকে নিয়ে সর্বদাই অসন্তুষ্ট —যেটা ওদের দৃঢ়ভাবে জীবনে আঘাত করেছে। ও ওদের মালিককে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে, বিশ্বাস করে ওদের যান্ত্রিক হৃদয়হীন শাসনই তাদের এ নিষ্ঠুর গন্তব্যে ঠেলে দিয়েছে। প্রায়ই ওরা সরকারি কর্মচারীদের প্রতি অশ্রাব্য কটুক্তি করত। ওরা ভাবত এ সরকারি কর্মচারীদের শ্রমিকদের প্রতি কোন সহানুভূতি নেই। নিত্য নৈমিত্তিক জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির জন্য লোক জড় করে সভা করত আর রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ মিছিল বার করত। অবশ্য এসব ব্যাপারগুলোর পেছনে যুক্তির মাধ্যমে একটা ব্যাখ্যা দেওয়া চলত। কিন্তু যে ব্যাপারটা কিছুতেই আমার বোধগম্য হত না, সেটা হল ওদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের তীব্র ঘৃণা। নিজেদের জাতটাকেই নিন্দা করত; এর মহত্ব নিয়ে উপহাস করত। ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুলে অতীতের পরম গৌরবমণ্ডিত মানুষগুলোকে সমালোচনার নোংরা নর্দমায় টেনে আনত।
তাদের নিকট আত্মীয়স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি বিরূপ মনোভাব, দেশ এবং জাতির প্রতি ঘৃণায় যে অপরিমেয় ক্ষতি সাধন করেছে তা পূরণ করা অসম্ভব। এটা একটা প্রকৃতি বিরুদ্ধ কাজ।
শুধু তাই নয়, এটা মানসিক এক ধরনের ব্যাধিও বটে; যেটাকে সাময়িকভাবে অর্থাৎ কয়েক মাস কয়েকদিনের জন্য সুস্থ করা সম্ভব। কিন্তু পরে ওদের সঙ্গে দেখা হলেই বুঝতে পারতাম যে আগে যা ভেবেছি যে ওদের মতের পরিবর্তন হয়েছে, তা সম্পূর্ণ নিল। ওরা ওদের আগেকার জায়গাতেই ফিরে গেছে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাদের সেই মানসিক পীড়া আবার নিষ্ঠুর থাবা বসিয়েছে।
আমি ক্রমেই বুঝতে পারি যে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক প্রেসও ইহুদীদের করতলগত। কিন্তু অন্যান্য প্রেসগুলোর যে একই অবস্থা এটা আগে কখনো বুঝতে পারিনি। সবচেয়ে উলঙ্গ সত্য হল, একটা সংবাদপত্রও ছিল না যাতে ইহুদীরা জড়িত নয় এবং যেটাকে সত্যিকারের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র বলা যেতে পারে। অন্ততপক্ষে এ ব্যাপারে আমার জ্ঞান এবং বিদ্যা বুদ্ধি অনুসারে আমি যা বুঝতাম।
অনেক চেষ্টার পর নিজের ভেতরের অলসতাটা ভেঙে আমি মার্কসিস্ট পত্রিকায় প্রকাশিত এ ধরনের প্রবন্ধগুলো পড়তে শুরু করি। কিন্তু তাতে ওদের প্রতি বিরূপতাই বাড়ে। এবং এরপরে আমি এসব লেখক আর প্রকাশকদের সম্পর্কে আরো বেশি খোঁজখবর নিতে শুরু করি।
এসব পত্রিকার প্রকাশক থেকে শুরু করে সবচেয়ে নিচু তলার কর্মী পর্যন্ত সবাই ইহুদী। মার্কসবাদী জননেতার নাম স্মরণে আসতে দেখি প্রায় সবাই এ একই সম্প্রদায়ের— রাজ পরিষদের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক সদস্যবৃন্দ থেকে শুরু করে ট্রেড ইউনিয়ানের সেক্রেটারী, পথরোধকারি, বিক্ষোভকারি, সবক্ষেত্রে এ একই সাজানো ছবি। আমার পক্ষে অস্টারলিটজু, ডেভিড, আড়লার,—এলেনবোগেন এবং অন্যান্য নামগুলো বিস্মৃত হওয়া কখনই সম্ভব নয়। একটা সত্য আমার সামনে ঝলঝল করে ওঠে; আমি যে দলটার সঙ্গে মাসাধিককাল মত বিরোধে লিপ্ত, তারা ওদেরই একটা ছোট শাখা বিশেষ। তবে শেষমেষ আমার একটা শান্তি ছিল যে ততদিনে জেনে গেছি ইহুদীরা আর যাহোক জার্মান নয়।
এবারে আমি আবিষ্কার করতে সমর্থ হই, কারা সেই প্রেতাত্মা যারা আমাদের জনসাধারণকে নিয়ত তাড়িত করে ছাইদানির দিকে নিয়ে চলেছে। ভিয়েনায় আমার বছর খানেকের প্রবাসী জীবনে বুঝতে পারি যে কোন শ্রমিকের এ বিষয়ে ধ্যান ধারণার শিকড় এত গভীর নয়। ক্রমে ক্রমে মার্কসীয় মতবাদ সম্পর্কে আমি একজন বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠি এবং এ বিষয়ে অর্জিত জ্ঞানকে, নিজের বিশ্বাসকে দৃঢ় করার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করি। বলতে আপত্তি নেই যে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই কৃতকার্য হয়েছি। এ বিশাল জনসাধারণকে অবক্ষয়ের পথ থেকে টেনে তোলা অসম্ভব নয়; তবে তার জন্য প্রয়োজন প্রচুর সময় এবং প্রচণ্ড অধ্যাবসায়।
কিন্তু একটা ইহুদীকেও তার স্থির মতবাদ থেকে এক চুল নড়ানো সম্ভব নয়।
আমি তখন ওদের শিক্ষার অবাস্তবতা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে শুরু করি। যে ছোট্ট গণ্ডিটা আমাকে ঘিরে থাকত, গলা না চেরা এবং কণ্ঠস্বর বসে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের একনাগাড়ে বুঝিয়ে যেতাম। আমি মনে করি শেষ পর্যন্ত মার্কসিস্ট মতবাদের ভয়াবহ দিকটার ছবি আমি তাদের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হব। যত আমার মতামতটাকে আমি প্রতিষ্ঠা করি, তত ওদের একগুঁয়েমিটা বেড়ে ওঠে।
তর্ক করতে করতে আমি ওদের কৌশলটা বুঝে ফেলি। তর্কের প্রথম পর্যায়ে ওরা বক্তার নিবুদ্ধিতার সুযোগের ফাঁক গলে বেরিয়ে পড়ে; কিন্তু যখন তর্কের জালে জড়িয়ে যুক্তির হালে আর পানি পায় না, তখন ভণিতা করে সহজে প্রতারিত হয়েছে, এমন ব্যক্তিরা যুক্তির জাল এড়িয়ে অভিনয় করে যেন বক্তার কিছুই ওরা বুঝতে পারছে না এবং প্রাণপণে চেষ্টা করে অন্যদিকে তর্কের স্রোতটাকে প্রবাহিত করার। তারা স্বতসিদ্ধ সত্যটাকে এড়িয়ে গিয়ে অন্য পথে কথাবার্তা বলে চলে। যদি এটাকে সহ্য করে নেওয়া হয়, তবে ওরা তর্কের ব্যাপারটাকে ভিন্নমুখী করে দিয়ে গোড়ার সমস্যার থেকে অন্য কোন বিষয় বস্তৃতে চলে যায়। যার সঙ্গে আগের বিষয়বস্তুর কোন সম্পর্কই নেই।
আবার যদি ওদের মূল তর্কের বিষয়ে টেনে আনার চেষ্টা করা হয়, ওরা আবার পালাবে সেই জাল থেকে। মোটকথা ওদের দিয়ে বিষয়বস্তুটার ওপরে কোন মন্তব্যই পাওয়া সম্ভব নয়। যখন কেউ শক্ত মুঠিতে এ তথাকথিত অবতারদের একজনকে পাকড়াতে চেষ্টা করে, জেলী বা আঠালো কাদার মত ঠিক আঙুলের ফাঁক দিয়ে সে গলে গিয়ে পরক্ষণেই আবার সেই কাদা বা জেলী জমে শক্ত জিনিসের অবয়ব ধরবে। যদি উপস্থিত জনতার উপস্থিতিতে বিরুদ্ধজনক পরিস্থিতিতে কারোর বিরুদ্ধপক্ষ যুক্তি স্বীকারও করে নেয়, এবং তা নিয়ে কেউ যদি ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে যে যাক শেষপর্যন্ত ওদের একটা নির্দিষ্ট জমিতে দাঁড় করান গেছে, তা হলে তার পরের দিনের জন্য তার কাছে অবাক করা কিছু লুকানো থাকবে। ইহুদীরা বড়ই বিস্মৃতিপরায়ণ। অর্থাৎ কাল যা ঘটেছে তা আজ ভুলে যেতে ওরা এতই ওস্তাদ যে তারা আবার গতকালের সেই অসংগতিপূর্ণ যুক্তিটাকেই তুলে ধরবে এমনভাবে যেন গতকাল তাদের সঙ্গে কোন আলোচনাই হয়নি। তখন যদি কেউ রাগ করে তাকে গতকালের কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দেয়,–সে এমন অবাক হওয়ার ভাণ করবে যেন তার কিছুই মনে নেই। শুধু একমাত্র তার যা স্মরণ আছে তা হল গতকাল সে তো প্রমাণই করে দিয়েছে যে তার যুক্তিগুলোই ঠিক। আমি তো এ অবস্থায় হতবুদ্ধি হয়ে যেতাম। আমাকে ঠিক কোনটা হতবুদ্ধি করে দিত,–তার বাগাড়ম্বরের প্রাচুর্য নাকি সুনিপুণভাবে মিথ্যেটাকে সত্য বলে পরিবেশন করার ভঙ্গি, তা বলতে পারব না। ক্রমে ক্রমে আমি তাদের ঘৃণা করতে শুরু করি।
তবু এসবগুলোর ভাল একটা দিক ছিল,–কারণ আমি যত বেশি এসব নেতাদের ব্যক্তিগতভাবে চিনতে পারি, (নেতা না বলে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির প্রচারক বলাই ঠিক) আমার নিজের লোকেদের প্রতি তত বেশি ভালবাসা বাড়তে থাকে, ঠিক সেই অনুপাতে। ওদের এ পৈশাচিক কুশলতা যেটা এ শয়তান মন্ত্রণাসভার সভ্যগুলোর কার্যকলাপ এবং কথাবার্তায় প্রদর্শিত হত, তাতে ওদের নিকটে হতভাগ্য পরাজিতদের পরাজিত হওয়ার জন্য কোন দোষ আমি দেখি না। সত্যি বলতে কি, এ প্রাদেশিক বিশ্বাসঘাতকগুলোর সঙ্গে কোনরকম সামঞ্জস্য রেখে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সত্য বলায় বিকৃত এ মুখগুলো, যারা নিজেদের উচ্চারিত কথা পরমুহূর্তেই অস্বীকার করে, পরক্ষণেই আবার মুক্তির ধ্বজা তুলে ধরতে তর্ক প্রসঙ্গে সেটাকেই ফিরিয়ে আনে, এরকম নোংরা জীবগুলোর বিরুদ্ধে তর্ক যুদ্ধে জয়ী হওয়ার প্রস্তাবটাও নিরর্থক। অসম্ভব তো বটেই। না, যত বেশি ইহুদীদের আমি চিনতে পারি, তত সহজে আমি সেই শ্রমিকদের মতামতের জন্য তাদের ক্ষমা করি। শেষে আমার মত হল এ যে শ্রমিকদের মধ্যে নিন্দনীয় কিছু নেই। কিন্তু যারা নিজেদের আপন লোকদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর কষ্টটুকু পর্যন্ত স্বীকার করতে নারাজ, তারা জাতির পরিশ্রমী সন্তানকে বিনা দ্বিধায় অবিচার স্বীকার করে নিতে বাধ্য করেছে, অপরদিকে একদল নিচুমনা লোভী এবং দুর্নীতিপরায়ণকে প্রশ্রয় দিচ্ছে, যাদের কোনরকমেই ক্ষমা করা উচিত নয়।
আমি নিত্যদিনের অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে মার্কসবাদীয় মতবাদের শিক্ষার উৎস মুখটা খুঁজতে আরম্ভ করি। কারণ এ মতবাদের ফলাফল আমি বিস্তারিতভাবেই জানতাম। সুতীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণে এ মতবাদের নিত্য বিস্তারও আমার নজর এড়ায়নি। কারও একটু কল্পনা শক্তি থাকলেই ব্যাপারটার ভবিষ্যত ফলাফল সম্পর্কে ধারণা করে নেওয়া কোন কষ্টসাধ্য ব্যাপারই নয়। শুধু একটাই জিজ্ঞাসা— এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতারা কি আজকের ফলাফল তাদের ভবিষ্যত দ্রষ্টার দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পেরেছিল? নাকি প্রতিষ্ঠাতারা নিজেরাই নিজেদের ভুলের জালে জড়িয়ে পড়েছে। আমার তো মনে হয় দুটোরই সম্ভাবনা আছে।
যদি দ্বিতীয় প্রশ্নটার উত্তর হ্যাঁ হয়, তবে প্রতিটি চিন্তাশীল ব্যক্তির উচিত তখনই এ দানবকে রজ্জবদ্ধ করা, যাতে ভবিষ্যতে আরো খারাপ কিছু না করতে পারে। কিন্তু যদি প্রথম প্রশ্নটার উত্তর যা হয়, তবে এটাকে স্বীকার করে নিতেই হবে যে এ মতবাদের প্রতিষ্ঠাতারা ইচ্ছে করেই জাতির মধ্যে এক মূর্ত শয়তানকে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছে। একমাত্র কোন দানবীয় অস্তিত্বই, হা–মানুষের নয়; এ ধরনের কোন সংগঠনের সৃষ্টি করতে পারে যার কার্যকলাপ ভবিষ্যতে মানব সভ্যতাকে বিলুপ্ত করে দিয়ে পৃথিবীটাকে সাহারা বানিয়ে ছাড়বে।
এ যদি ব্যাপারটা হয়ে থাকে, তবে এর প্রতিকার হল সমস্ত মনুষ্যশক্তি, বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তি দিয়ে এর বিরোধিতা করা এবং পুরো ব্যাপারটাকেই ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে দেখা কার দিকে ভাগ্যদেবী তার প্রসন্নতার হাত বাড়ায়।
সংগ্রামের মূল সূত্রগুলো জানার জন্য আমি এ তথাকথিত প্রবন্ধ সম্পর্কে আরো বেশি সংবাদ সগ্রহ করতে শুরু করি। সত্যি বলতে কি, আমার উদ্দেশ্যের কাছাকাছি আমি অনেক তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাই। এত শীঘ্র যে পৌঁছাব এটা আমিও আশা করিনি। আসলে ইহুদীদের ব্যাপারে ততদিনে আমার জ্ঞান চক্ষু খুলে গেছে। এতদিন পর্যন্ত ইহুদীদের সম্পর্কে আমার জ্ঞান ছিল ভাসা ভাসা। এ নতুন অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে আমি সত্যিকারের বিষয় বস্তুটার বক্তব্যটায় তথাকথিত সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির অবতারদের লিখিত আদর্শবাদীতার থেকে কতখানি দূরে, এ সত্যটা বুঝতে পারি। কারণ ততদিনে ইহুদীদের ভাষা হৃদয়ঙ্গম করতে আমি সক্ষম হয়েছি। ইহুদীরা ইচ্ছে করেই এমন কৌশলে তাদের বক্তব্য রাখত যাতে ভাষার কারসাজির জাল ভেদ করে কেউ ওদের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে না পারে। সুতরাং একমাত্র ওদের লেখাগুলোর বিশ্লেষণ করেই তা ধরতে পারা সম্ভব। এ জ্ঞানই আমার ভেতরে সবচেয়ে বেশি মানসিক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। একজন হৃদয়বান জাতীয় সংস্কারমুক্ত শহরবাসী থেকে কট্টর ইহুদী বিরোধী করে তোলে।
মাত্র একবার হ্যাঁ, শেষবারের মত আমি নিরাশার চিন্তায় নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করি, যা আমাকে কিছু সময়ের জন্য উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল।
আমি ইহুদীদের অতীতের দীর্ঘ ইতিহাসের কার্যাবলী বিশ্লেষণ করে রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে নিজেকেই জিজ্ঞাসা করি, কোন দুয়ে কারণে যেটা আমাদের হতভাগ্য নশ্বরদের বোধগম্যের বাইরে, পরিণতির অপরিবর্তনীয় আদেশে প্রছন্ন রয়ে গেল। আর জয় সুনিশ্চিতভাবে চলে যাবে এ ছোট্ট একটা জাতির হাতে। হতে পারে পৃথিবীতে এতদিন ধরে যারা বসবাস করে এসেছে, পৃথিবীর নিকট তারা তাদের ঋণ কি পরিশোধ করেনি? নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য আমরা এ যে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চলেছি তার ভিত্তিমূল কি বাস্তবতার মাটিতে পোথিত? নাকি এটা শুধু একটা রঙিন কল্পনা? আমি যত বেশি মার্কসীয় মতবাদ সম্পর্কে অনুধাবন এবং বিশ্লেষণ করি, ভাগ্যই আমাকে এর উত্তর দিয়ে দেয়। ইহুদীদের কার্যকলাপ এদের সঙ্গে কতখানি জড়িত তা স্পষ্ট চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেয়।
ইহুদীদের মার্কসীয় মতবাদ প্রকৃতির সম্ভ্রান্ত আদর্শগুলো থেকে লোকগুলোকে বর্জন করে। এভাবে ওদের শিক্ষা জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা থেকে সাধারণ মানুষকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। এবং এর অর্থ মানুষের অস্তিত্ব এবং সভ্যতাটার ভিত্তিমূলটাকেই প্রচন্ডভাবে নাড়া দেওয়া। যদি মার্কসীয় মতবাদকে জীবনের ভিত্তিমূল বলে সারা পৃথিবী মেনে নেয়, তবে মানব মনের পুরো ধ্যান ধারণাটাই অদৃশ্য হয়ে যাবে। এবং এ ধরনের কোন মতবাদকে মেনে নেওয়ার অর্থই হল নিজেদের মধ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা, যা এ পৃথিবী নামক মধ্যগ্রহের বাসিন্দাদের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে ছাড়বে।
সুতরাং ইহুদীরা যদি ওদের এ মার্কসীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠায় পৃথিবীতে কোনরকমে জয়ী হতে পারে, তবে সেদিন হবে মানুষের ইতিহাসের শেষদিন। এ উপগ্রহ আবার তাহলে জনপ্ৰাণীহীন মহাশ্মশান হিসেবে তার অক্ষরেখা ধরে পরিক্রমা করবে, যা আজ থেকে কোটি কোটি বছর আগে করত।
আমি বিশ্বাস করি যে আমার ধ্যান-ধারণা এবং চিন্তাধারা সেই সর্বশক্তিমানের দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং ইহুদীদের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়ানোই হল ইশ্বরের আপন হাতে সৃষ্ট মহান শিল্পকর্মকে রক্ষা করার একমাত্র পথ।
০৩. ভিয়েনায় প্রবাসের দিনগুলোয় আমার
রাজনৈতিক চিন্তাধারা তিরিশ বছর বয়স হবার আগে কোন পুরুষের প্রকাশ্যে কোন রাজনৈতিক ঘটনাতে অংশগ্রহণ করা উচিত নয় বলেই আমি মনে করি। অবশ্য প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের মত এক্ষেত্রেও যদি ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা তার থাকে, তবে তা স্বতন্ত্র কথা। এটা বলাবাহুল্য আমার মতামত। এর কারণ হল তিরিশ বছর পর্যন্ত মানুষের মানসিকতাটা গড়ে ওঠে দৈনন্দিন যেসব সমস্যার উদ্ভব হয়, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলো পর্যবেক্ষণ করে, সেসব অভিজ্ঞতাগুলোকে উল্টেপাল্টে এদিক ওদিক সরিয়ে সে একটা নির্দিষ্ট চিন্তায় স্থির হতে পারে; আর এটাই তাকে ভবিষ্যত রাজনৈতিক চিন্তাধারার ভিত্ গড়তে সাহায্য করে। তার পক্ষে সব বিষয়ে মনস্থির করে একটা নির্দিষ্ট পথ নেওয়া সম্ভব হয়। একজন পুরুষের পক্ষে প্রথম উচিত হল সাধারণ জ্ঞানের একটা ভান্ডার নিজের মধ্যে গড়ে ভোলা, যাতে জীবন সম্পর্কে তার নিজস্ব চিন্তাধারার একটা সুসংবদ্ধতা লাভ করতে পারে। অর্থাৎ যাকে এককথায় জীবন দর্শন বলে। তাহলে তার একটা নিজস্ব মানসিক ব্যারোমিটার গড়ে ওঠে, যেটা ছাড়া তার পক্ষে দৈনন্দিন কোন সমস্যা সম্পর্কে নিজের বিচার বিবেচনা গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। এবং এটাই তাকে কোন রাজনৈতিক বিষয়ে দৃঢ় এবং স্থির সংকল্প নিতে সাহায্য করবে। আপাতদৃষ্টিতে এ ধরনের পুরুষ তার রাজনৈতিক চরিত্রের দিক থেকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণের যোগ্যতা রাখে।
এ ধরনের মানসিক জমি প্রস্তুত না করে যদি কেউ রাজনীতিতে প্রবেশ করে, তবে সে উভয় সংকটে পড়তে বাধ্য। প্রথমে সে উপলব্ধি করবে জরুরী কতগুলো ঘটনায় তার চিন্তাধারা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত, তার চিন্তাধারা অসমর্থনীয় হওয়াতে তার আগের মতবাদ সমর্থন না পাওয়ায় স্বভাবতই তাকে আরও ভাল জ্ঞান এবং পরিপূর্ণ বিচারের আশায় ছুটতে হবে। যদি সে তার আগের চিন্তাধারাটাকে আঁকড়ে পড়ে থাকে, তবে অতি শীঘ্র এমন এক সংকটপূর্ণ জায়গায় এসে দাঁড়াবে যে সেটা অতিক্রম করা তার পক্ষে দুঃসাধ্য। কারণ তা হলে তার চিন্তাধারায় এত বেশি অসংগতি দেখা যাবে যে তাকে কেউ নেতা বলে আগের মত মানবে না। আর তার অধীনস্থ পাটির লোকেরা সহজেই বুঝে ফেলবে যে যাকে তারা এত দিন নেতা বলে মেনে নিয়েছে, তার চরিত্রে পরিবর্তন তাদের মধেও নৈরাশ্য এনে দেবে, যেটা তাদের নেতা আগে কখন সহ্য করত না।
যদি সে দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করে যেটা ইদানীং অহরহ ঘটে থাকে, সেক্ষেত্রে। জনসাধারণকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির পেছনে নিজের মানসিক প্ররোচনা কাজ করে না। এটার উর্ধ্বগতিতে তাকে বেশি করে ভাবিয়ে তোলে। এবং বিষয়বস্তুর ওপরেই ভাসিয়ে নিয়ে বেড়ায়। ভেতরে ঢুকতে দেয় না। সুতরাং আত্মরক্ষার খাতিরে তাকে নোংরা পথ বাধ্য হয়েই অবলম্বন করতে হয়। যেহেতু সে নিজেই তার স্বপ্নের পেছনে দৃঢ়ভাবে। দাঁড়ায় না, তাই কোন মানুষই মনেপ্রাণে সেই মতবাদকে বিশ্বাস করে না এবং তার জন্য
জীবন দিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রস্তুতও হয় না। তখন সে তার অনুবতীদের কাছ থেকে। আরও বেশি কিছু দাবি করে। সত্যি বলতে কি, যত বেশি পরিমাণে তার নিজের চিন্তাধারার স্বচ্ছতা এবং মানসিক গতিবেগ হ্রাস পায়, তত বেশি চাপ আসে তার অনুগত কর্মীদের ওপর। শেষপর্যন্ত সত্যিকারের নেতৃত্বের খোলসটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রাজনীতির সঙ্গে সে শুধু খেলাই করে। এভাবে দিনে দিনে তার দৈনন্দিন কাজকর্মের অসংলগ্নতা সামঞ্জস্যের পরিপূরক হয়ে দাঁড়ায়। এর সঙ্গে যোগ হয় অসত্যতা আর একগুয়েমী মনোভাব,—যেটার সমাপ্তি হওয়া সম্ভব একেবারে চরমে উঠে। দলিত মানুষদের দুর্ভাগ্যের জন্য এ ধরনের লোকেরা নিজেদের দুধের বোতলটাকে দৃঢ় হাতে ধরে নিয়ে বসে পার্লামেন্টে, আর নিজের সন্তান-সন্ততি এবং পরিবারের সমস্ত রকম বিলাসিতার খরচ জোগাড় করতেই রাজনৈতিক খেলা দেখায়।
পরিবারের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে তার রাজনৈতিক খেলাও বাড়তে থাকে। সে কারণে যে মানুষ নিজেকে রাজনীতির খেলায় যত বেশি দক্ষ বলে মনে করে, নিজেই সে নিজের তত বড় শত্রু। প্রতিটি নতুন সংগ্রামের ক্ষেত্রে সে নিজেকেই ধাক্কা দিয়ে নিচের দিকে নামিয়ে নিয়ে চলে এবং তার চেয়ে যোগ্যতর যে কোন ব্যক্তিকেই সে নিজের আলোয় অযোগ্য বলে মনে করে।
এ সমস্যার গভীরে ঢোকার সময় এ ধরনের নিচ লোকগুলো পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রে কিভাবে ওপরে ওঠে তার বিশদ ব্যাখ্যা করব।
একজন মানুষ যখন তার ত্রিশ বছরের বন্দরে পা রাখে, তখন তার সমুদ্রযাত্রার অনেক বাকি। অর্থাৎ তার সামনে শিক্ষণীয় অনেক কিছু পড়ে থাকে। এবং সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে তার আগের চিন্তাধারাটাকেই আঁকড়ে ধরে বসে থাকে,—যেটা তার জীবনের সংগে ততদিনে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে গেছে। নতুন যেগুলো সে শোনে, সেগুলো আগেকার আদর্শগুলোকে পরিত্যক্ত করতে পারে না, বরং মনের অবচেতনে গভীরভাবে গেঁথে দেয়। তার সহকর্মীরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না যে তারা তার চিন্তাধারা বা আদর্শ নিয়ে প্রতারিত হচ্ছে। উপরন্তু তাদের নেতাদের নতুন চিন্তাধারাকে পরিপাক করার ক্ষমতা দেখে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে। সুতরাং তার অনুগামীদের মধ্যে নেতার মতবাদে আরও বিশ্বাস আনে। তাদের চোখে এ ধরনের প্রতিটি ঘটনা তাদের নেতার উন্নতির স্বর্ণোজ্জ্বল স্বাক্ষর।
একজন নেতা যাকে একদিন নিজের ভুলের ভিতের ওপর স্থাপিত পটভূমি ছেড়ে দিতে হয়, তখন সে আবার সম্মানের সঙ্গে কাজ শুরু করতে পারে, যদি তার পক্ষে ভুলগুলোকে ভুল বলে মেনে নিয়ে বাস্তবকে স্বীকার করার মত মানসিক জোর থাকে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে গণজীবনের রাজনৈতিক কার্যকলাপ থেকে তার সরে আসাটাই উচিত। একবার যখন সে ধ্বংসের পথে পা বাড়িয়েছে, দ্বিতীয় বারেও যে সেদিকে সে যাবে না তার স্থিরতা কোথায়। যাহোক এক্ষেত্রে অন্তত তার অনুগামীদের কাছ থেকে নৈতিক দাবি স্বপক্ষে থাকা উচিত নয়।
বর্তমান রাজনৈতিক নেতাদের চারিত্রিক দুনীতিপরায়ণতার এগুলো হল প্রধান কারণ। তাই আজকের রাজনৈতিক আকাশে একজনকেও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর, যে এ দুর্নীতির আওতার বাইরে নিজেকে রেখে আলোর গতিপথে এগিয়ে চলেছে।
অবশ্য অতীতের সেই দিনগুলোয় রাজনৈতিক সমস্যাগুলোর চিন্তার পেছনেই আমি বেশি সময় খরচ করতাম; কিন্তু তবু আমি রাজনীতিতে প্রকাশ্যভাবে অংশ নেওয়ার থেকে অতি সতর্কভাবে বিরত থাকতাম। যে সমস্যাগুলো অবিরত আমাকে দংশনে ক্ষত বিক্ষত করত, সেগুলো নিয়ে সীমাবদ্ধ অতি স্বল্পসংখ্যক লোকের কাছে মুখ খুলতাম, আলোচনা করতাম, সীমাবদ্ধ এ গম্ভীর আলোচনা চালানোর সুফল অনেক। নিজে কথা বলার চেয়ে আমাকে ঘিরে থাকা স্বল্পসংখ্যক লোকগুলোর চিন্তাধারা এবং মতামত বুঝতে অনেক বেশি সচেষ্ট থাকতাম। যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ ধরনের চিন্তাধারা এবং মতামত সে করলে ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত; তবু এ পথেই আমি মানুষ সম্পর্কে আমার জ্ঞান বাড়িয়েছি। ভিয়েনায় এ ব্যাপারে যত সুযোগ আমি পেয়েছি জার্মানদের সম্পর্কে জ্ঞান বাড়ানোর, অন্য কোথাও সে সুযোগ পাওয়া সম্ভব নয়।
জার্মানির চেয়ে প্রাচীন ভাণুবিয়ান সাম্রাজ্যের রাজনীতিতে অনেক বেশি বৈচিত্র পরিধি বিস্তৃত ছিল। অবশ্য প্রুশিয়ার কিছুটা অংশ, হামবুর্গ এবং নর্থ-সীর প্রত্যন্ত প্রদেশের কয়েকটা জেলা ছাড়া। যখন আমি অস্ট্রিয়ার কথা বলি, তখন অবশ্য হাবুসবুর্গ সাম্রাজ্যের কথাই বোঝাই। কারণ সেই সুবিস্তীর্ণ জার্মান অধ্যুষিত হাবুসবুর্গ সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের রাজনৈতিক জীবনের মধ্যকার সাংস্কৃতিক জীবনটা ছিল নিছকই কৃত্রিম। যত দিন যেতে থাকে তত যেন অস্ট্রিয়ান সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি হাবুসবুর্গ সাম্রাজ্যের বীজাণু ভর্তি ইটের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।
বংশগত রাজকীয় সম্প্রদায় হল সে সাম্রাজ্যের হৃদয়স্বরূপ। আর সে হৃদয়ই দেশের রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রক্ত সঞ্চালনের দ্বারা নাড়ীর গতি ঠিক রাখে। এ সাম্রাজ্যের-হৃদয়ের মস্তিষ্ক এবং ইচ্ছাশক্তি হল ভিয়েনা। তখনকার দিনের ভিয়েনার চালচলন দেখে মনে হত যেন মুকুটহীন রাণী, যার আঙুল সঙ্কেতে বিভিন্ন জাতিরা মুহূর্তে একটা পিণ্ডে পরিণত হয়ে হাবুসবুর্গ রাজদণ্ডের নিচে মাথা পেতে দিত। রাজধানী শহরের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে রাজ্যগুলোর বার্ধক্যজনিত অবক্ষয়তা নজর এড়িয়ে যেত।
যদিও ভেতরে ভেতরে তখন সে সাম্রাজ্য ক্ষয়িত। কারণ আর কিছুই নয়, বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব। কিন্তু বাইরের জগৎ থেকে বিশেষ করে জার্মানির নজরে তা পড়ত না। কারণ তাদের দৃষ্টি তখন সেই সুন্দর শহরের দিকেই একমাত্র নিবন্ধ। সেই কুয়াশাচ্ছন্ন দৃষ্টির প্রধান কারণ হল শহর ভিয়েনা— তখন তা গৌরবের উত্তুঙ্গ শীর্ষে। সুযোগ্য মেয়রের সুন্দর প্রশাসনে সেই প্রাচীন শহর যেন যৌবনের নতুন সাজে সুসজ্জিত।
সর্বশেষে যে মহান জার্মান সাধারণ জনতার মধ্য থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল এবং পুরো পূর্বদিকটা কজা করতে পেরেছিল, সত্যিকারের নেতা যদিও তাকে বলা যায় না, তবু এ ডক্টর লুইগের মেয়র হিসেবে এ সাম্রাজ্যের রাজধানীটিতে এতটুকু প্রাণ সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিল যে অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক উভয় দিক থেকে সম্পূর্ণ সাম্রাজ্যের হৃদয়টাই নতুন উদ্দীপনায় জেগে উঠেছিল। সেই কারণে তৎকালীন রাজনীতিজ্ঞদের থেকে নেতা হিসেবে তার স্থান অনেক উঁচুতে।
এটাও সত্যি যে এ ধরনের পাঁচ মিশেলী জাতির সমন্বয়ে গঠিত অস্ট্রিয়া শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক অক্ষমতার জন্যেই ভেঙে পড়ে। অসম্ভব পরিস্থিতির পরিণতিই হল এ ভঙ্গুর অবস্থা। পঞ্চাশ লক্ষ বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে গঠিত কতগুলো প্রদেশকে, যারা প্রতিনিয়ত সংঘর্ষে লিপ্ত দশলক্ষ লোকের একটা দেশ হয়ে তাদেরকে শাসন করা অসম্ভব। যদি শেষপর্যন্ত বিশেষ সংগঠিত কোন পরিকল্পনা হাতে থাকে।
অস্ট্রিয়ায় বসবাসকারী জার্মানদের চিন্তাধারা সব সময়েই উঁচু ছিল। বিরাট একটা সাম্রাজ্যে বসবাস করে এ ধরনের পরিস্থিতিতে নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে সদা সর্বদাই সচেতন থাকত। অস্ট্রিয়ার এতগুলো প্রদেশের মধ্যে একমাত্র ওরাই একফালি জমি পেরিয়ে সীমান্তের ওপারের দেশটায় দৃষ্টি মেলে দিত। সত্যি বলতে কি, নিয়তি তাদের নিজেদের পিতৃভূমির থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিলেও, তাদের ওপর সম্পর্কিত কর্তব্য তারা ভোলেনি। এ কর্তব্য বা দায়িত্ব হল স্বদেশপ্রেম, যা তাদের পূর্বপুরুষেরাও মনেপ্রাণে পোষণ করে এসেছে। তবে এটাও স্মরণীয় যে অস্ট্রিয়ার জার্মানরা মনেপ্রাণে সেই পথের প্রয়াসী হতে পারেনি। কারণ হৃদয় এবং মস্তিষ্ক তাদের মাতৃভূমির আত্মীয়স্বজনের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে দেয়নি। সে কারণে সমস্ত শক্তি তাদের পক্ষে বিনিয়োগ করা সম্ভব ছিল না।
অস্ট্রিয়ার জার্মানদের মানসিক উদারতাও ছিল অন্যান্যদের চেয়ে বেশি। তাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ সেই মিশ্রিত সাম্রাজ্যের প্রায় প্রতিটি শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত। অধিকাংশ বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের দ্বারাই পরিচালিত। শিল্প বিশেষজ্ঞ এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেশিরভাগ তাদের মধ্যে থেকেই এসেছে। এমন কি বৈদেশিক বাণিজ্যও তাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত; বিশেষ করে ইহুদীদের এ জগতে ঠাঁই ছিল না বললেই হয়। শুধু তাই নয়, অস্ট্রিয়ার বসবাসকারি জার্মানরাই বিভিন্ন প্রদেশগুলোকে একসূত্রে গ্রথিত করে রেখেছিল। তাদের সামরিক কলাকৌশলের খ্যাতি দেশের সীমান্ত পেরিয়ে বহুদূরে গিয়েছিল। যদিও সে বাহিনীর অধিকাংশ সৈনিক জার্মান, তবু তাদের রাখা হয়েছিল হেরজে-গাভিনা এবং ভিয়েনা অথবা গেলিসিয়া প্রভৃতি জায়গায়। হাবুসবুর্গ সামরিক বাহিনীর অফিসার এবং বেসামরিক অফিসারবৃন্দ প্রায় সবাই ছিল জার্মান। বিজ্ঞান এবং শিল্পকলাও ছিল তাদেরই হাতে। তথাকথিত আধুনিক শিল্পকলার নামে আবর্জনা বিশেষ; যা এমন কি নিগ্রোদের পক্ষেও সৃষ্টি করা সহজ। বাকি উঁচু দরের শিল্পকর্ম বলতে যা বোঝায় সবাই প্রায় জার্মান গোষ্ঠী থেকেই সৃষ্টি হত। সঙ্গীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য বা অঙ্কন শিল্প প্রভৃতি যেসব শিল্পকর্ম দ্বারা শহর ভিয়েনা সমৃদ্ধ, তার অধিকাংশের সৃষ্টিকর্তা ছিল অস্ট্রিয়ার বসবাসকরি জার্মানরা। এবং এ ভান্ডার নিঃশেষিত হবার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছিল না। সর্বপরি, এ জার্মানরাই বৈদেশিক নীতির নির্ধারক ছিল, যদিও খুবই স্বল্প পরিমাণে হাঙ্গেরীয়ানরাও এ বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে সহায়তা করত।
কিন্তু সমস্ত প্রদেশগুলোকে এক সূতোতে বেঁধে রাখার জন্য প্রাথমিক উপকরণ যা দরকার তারই অভাব ছিল অত্যন্ত বেশি।
এ বিভিন্ন প্রদেশের জাতিকে এক জায়গায় ধরে রাখার মাত্র একটাই পথ। অস্ট্রিয়ার প্রদেশগুলোকে অন্তশক্তি দিয়ে শাসনের মাধ্যমে শক্তিশালী এক কেন্দ্রের নিচে নিয়ে আসা। অন্য আর কোন পথই ছিল না যার দ্বারা এর অস্তিত্ব রক্ষা করা যায়।
মাঝে মধ্যেই ওপর মহলে এ সত্য আবিস্কার হত। কিন্তু তা কিছুক্ষণের বা কয়েকদিনের জন্য। এক সময় সবাই তা ভুলে যেত বা ইচ্ছে করে ভুলে থাকত। এ দিনের আলোর মত স্পষ্ট সত্যটাকে। কারণ এটাকে স্বীকার করে নেওয়ার মত কষ্টটাকে দৃঢ়ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে বাঁধার চিন্তাধারা কখনই কার্যকর করা হত না। এ চিন্তাধারাটাকে কার্যে পরিণত করার মত শক্তিশালী কোন কেন্দ্রও ছিল না। এখানে মনে রাখা সবিশেষ প্রয়োজন যে তকালীন অস্ট্রিয়ার অবস্থা বিসমার্ক শাসিত জার্মানির মত ছিল না। জার্মানির সমস্যা তখন একটাই; তা হল রাজনৈতিক। কারণ বিসমার্কের সময় জার্মানির সাংস্কৃতিক পটভূমিতে কোন মিশেল ছিল না। সাম্রাজ্যের প্রতিটি সদস্য একই জাতির বা গোষ্ঠীর; শুধু স্বল্প সংখ্যক কয়েকটা টুকরো ছাড়া।
অস্ট্রিয়ার গৃহ ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। হাঙ্গেরী ব্যতীত রাজনৈতিক কোন ধারা ছিল না, এবং এটা প্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছিল। যদি থেকেও থাকে, তবে তা ইতিমধ্যে হয় ধুয়ে মুছে লুপ্ত হয়েছে, নয় যুগের অন্ধকারে তলিয়ে গিয়ে তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। সর্বপরি এ যুগটা হল জাতীয়তাবাদী উত্থানের প্রাক্-মুহূর্ত। আর সে কারণে হাবুসবুর্গ রাজদণ্ডের নিচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দেশগুলোও তার স্বাদ ইতিমধ্যে পেয়ে গেছে। এ নতুন উদ্ভুত জাতীয়তাবাদী মতাদর্শকে দমন করে রাখাও অসম্ভব। তার কারণ হল সীমান্ত ঘেঁষা সাম্রাজ্যগুলো এ নতুন জন্ম দেওয়া প্রদেশগুলো হাবুসবুর্গ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশগুলোর আত্মীয় হওয়াতে এর ছোঁয়া লেগে সাম্রাজ্য রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। অস্ট্রিয়ার বসবাসকারী জার্মানদের থেকে ওদের হাবুসবুর্গ সাম্রাজ্যের ওপর প্রভাব ছিল অনেক বেশি।
এমন কি ভিয়েনা পর্যন্ত এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খুব বেশি দিন নেতৃত্ব দিতে পারে নি। তখন বুদাপেস্তও ধীরে ধীরে ইউরোপের একটা প্রধান নগর হিসেবে সবেমাত্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন কেন্দ্রীয় শক্তিগুলোকে একসঙ্গে বেঁধে না রেখে, কোন একটা বিশেষ শক্তিকে আরও বেশি শক্তিশালী করা। কিছুদিনের মধ্যে প্রাণও বুদাপেস্তের মত একই লাইনে গিয়ে ভেড়ে। পেছনে পেছনে আসে লেমবার্গ, লাইখ আর অন্যান্যরা। এসব প্রাদেশিক শহরগুলো ধীরে ধীরে রাজধানীতে রূপান্তর হওয়ায় এদের এক পৃথক সাংস্কৃতিক জীবনও গড়ে ওঠে। এবং সাধারণ জনতার মাধ্যমে। ওরা নিজেদের সাংস্কৃতিক দৃঢ় ভিত স্থাপন করে। এক সময় সাধারণ জনতার স্বার্থের চেয়ে নিজেদের স্বার্থটাই উঁচু হয়ে ওঠে, যখন সমস্ত পর্যায়টা এক ছন্দে ওঠে, তখনই অস্ট্রিয়ার ভাগ্য ওদের কাছে বন্ধক পড়ে।
বিশেষ করে দ্বিতীয় যোসেপের মৃত্যুর পর সমস্ত ব্যাপারটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ স্বাভাবিক দ্রুতগতি নির্ভর করে অনেকগুলো বিষয়ের ওপর, কয়েকটা বিষয়ের জন্য স্বয়ং রাজা দায়ী। বাকিগুলো অবশ্য বৈদেশিক নীতির গর্ভে উদ্ভূত।
অস্ট্রিয়ার প্রদেশগুলোকে বিশেষ কোন একটা কেন্দ্রীয় শক্তি ছাড়া একসূতোয় বাধা। একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়ে। অন্য কিছু করার আগে সমস্ত প্রদেশগুলোয় একমাত্র একটা ভাষার প্রচলন করার দরকার। যার মাধ্যমে সরকারি কাজকর্ম চালানো সম্ভব হবে। এ একটা সুতো দিয়েই একমাত্র রাজকীয় টুকরোগুলোকে একসঙ্গে জোরে বাঁধা যায়। সুতরাং পুরো শাসন ব্যবস্থাটাই এমন এক যন্ত্রের মাধ্যমে বাঁধতে হবে, যা ছাড়া রাজনৈতিক একতা সম্ভব নয়। এভাবেই প্রতিটি বিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একই মন্ত্র জপ করে মনের এমন এক স্তরে গেঁথে দিতে হবে যে নিজেরা নিজেদের একই দেশের নাগরিক বলে মনে করে। এটা অবশ্য দশ-বিশ বছরের মত অল্প সময়ের মধ্যে করা সম্ভব নয়। এ প্রচেষ্টা শতাব্দী ধরে চালানোর প্রয়োজন, বিভিন্ন উপনিবেশ স্থাপন করার সময় যেমন মানসিক ধৈর্যের প্রয়োজন সাময়িক উৎসাহের চেয়ে অনেক বেশি।
সুতরাং এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে এ পরিবেশে দেশের শাসনব্যবস্থা একত্র আদর্শে দৃঢ় হাতে পরিচালিত হওয়া উচিত।
অন্য প্রদেশের চেয়ে পুরনো অস্ট্রিয়ার অস্তিত্ব রাখার জন্য প্রয়োজন ছিল শক্ত এবং সুপরিচালিত সরকারের। হাবুসবুর্গ সাম্রাজ্যের পরিচালনার ব্যবস্থার মধ্যে সবচেয়ে অভাব ছিল মানুষ যে বাঁধনে পরস্পরকে বাধে, সে বন্ধনের। এবং কোন জাতির যদি ভিত মানবজাতির বন্ধনের ওপর গড়ে ওঠে তবে সরকার পরিচালন ব্যবস্থায় অনভিজ্ঞ হলেও সহসা তা ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা নেই। যখন কোন প্রদেশ বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে, তখন তাদের স্বাভাবিক জড়তা পরস্পরকে কুশাসন এবং অপরিণত শাসনব্যবস্থা; সত্ত্বেও বিস্ময়করভাবে দীর্ঘদিন ধরে রাখে।
অনেক সময় মনে হয় যে এ রাজনৈতিক দেহ থেকে জীবনের আদর্শগুলোই হয়ত বা মরে গেছে। কিন্তু যথা সময়ে দেখা যায় সে মৃতদেহগুলো আবার হঠাৎ জেগে উঠে ২ কলরব করতে শুরু করেছে, এবং এ রকম অবিনশ্বর শক্তি দেখে পৃথিবী বিস্ময় মানে।
কিন্তু যে দেশের লোকসংখ্যা মিশ্রিত নয়, সে দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। কারণ শাসন ব্যবস্থা সেখানে একার হাতে থাকলেও রক্ত তো এক নয়। যদি এমন সরকার বহাল থাকে যা ঘুমিয়ে থাকা একটা জাতিকে জাগানোর পক্ষে দুর্বল, তবে তা তাদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয় যতক্ষণ না পর্যন্ত দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি দ্বারা কেন্দ্রীয় কোন সরকার পরিচালিত হয়। এ ঘুমিয়ে থাকা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিপদের সম্ভাবনা কম থাকে যদি শতাব্দী ধরে একই শিক্ষা, এক ট্রাডিসন এবং একই ধরনের স্বার্থ থাকে। সরকার যত নবীন হয়, কেন্দ্রের ওপর তার নির্ভরশীলতাও তত বাড়ে। যদি তাদের ভিত্ কোন সক্ষম নেতার ব্যক্তিত্বের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে, তবে সে নেতা বা ব্যক্তিত্বের অপসারণের সংগে সংগে সে অট্টালিকা ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা। কারণ ব্যক্তিত্ব বিরাট হলেও সে তো একক। কিন্তু শতাব্দী ধরে সহশিক্ষা থাকলেও আমি যে সব ব্যক্তিত্বের কথা বলছি তাদের এড়িয়ে যাওয়া সবসময় সম্ভব নয়। অনেক সময় তারা হয়ত বা সুপ্ত অবস্থায় থাকে, কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতা দেখলেই হঠাৎ তারা জেগে ওঠে। এবং সে সময় একক ব্যক্তিত্বের স্বার্থের স্রোতে শতাব্দী ধরে চলে আসা শিক্ষা বা ট্রাডিসন ভেসে যেতে বাধ্য।
এ সব সত্যগুলোর অবলুপ্তিই হল হাবুসবুর্গ শাসকদের অপরাধ বিশেষ।
একমাত্র একজন হাবুসবুর্গ শাসকের চোখের সামনে ভবিতব্যের আলোটা দপ্ করে জ্বলে ওঠে, যাতে হাবুসবুর্গ সাম্রাজ্যের ভবিষ্যত উজ্জ্বল হয়। কিন্তু সে হঠাৎ আলোর ঝলকানিও চিরতরে নিভে যায়।
যোসেপ দ্বিতীয়: জার্মান জাতির রোমান সম্রাট যখন অত্যন্ত উদ্বিগ্নতার সঙ্গে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল, তখন অবশ্য পুরো ব্যাপারটাই সীমান্তের ওপরে দাঁড়িয়ে। ক্ষয়িষ্ণু, মিশ্রিত দেশবাসীর দ্বারা সৃষ্ট বিরাট বিরাট ঘূর্ণাবর্তগুলি যেন হাঁ করে পুরো সাম্রাজ্যটাকেই গিলতে আসছে। যদি শেষ মুহূর্তে তার পূর্বপুরুষদের অবহেলার প্রতিকার এ মুহূর্তেই কিছু করা যায়। অতি মানবীয় মানসিক শক্তিতে দ্বিতীয় যোসেপ তার পূর্বপুরুষদের অবহেলা এবং বোকামির মোকাবিলা করে, মাত্র এক যুগের মধ্যে সে প্রাণপণে চেষ্টা করে শতাব্দী ধরে ফুটো হওয়া নৌকাটাকে সারাতে। যদি তার ভবিতব্য তাকে আর মাত্র চল্লিশটা বছর পরিশ্রম করার সুযোগ দিত, এবং পরবর্তী দুটো বংশধর তার ইঙ্গিত কাজ চালিয়ে যেতে পারত, তবে হয়ত বা আশ্চর্যজনক কিছু ঘটে যাওয়া বিচিত্র ছিল না। কিন্তু মাত্র দশ বছরের শাসনকার্যের পর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে, তার প্রগতিমূলক কার্যাবলী ও দৃষ্টিভঙ্গিও কবরের অন্ধকার গহ্বরে চিরতরে প্রোথিত হয়ে যায়; যারা আর কোনদিন প্রাণের ইসারা নিয়ে জেগে ওঠেনি। সেগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত তার পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে না ছিল ইচ্ছাশক্তি, না কর্মক্ষমতা।
সমগ্র ইউরোপে নব বিপ্লবের সঙ্গে ধীরে ধীরে তা অস্ট্রিয়াতেও ছড়িয়ে যায়। কিন্তু সেই আগুনের শিখা ভালভাবে প্রজ্জ্বলিত হওয়ার আগেই তা জ্যোতিহীন হয়ে পড়ে। কারণ আর কিছুই নয়, এ আগুনের উৎপত্তি হয়েছিল মিশ্রজাতিদের মধ্য থেকে। সুতরাং জোর থাকবে কোথায়। ১৮৪৮ সালের ইউরোপের বিপ্লবের সময় যখন সমগ্র ইউরোপ শ্রেণী সংগ্রামে রত, তখন অস্ট্রিয়ায় এর রূপ ছিল পরস্পরের জাতি বিদ্বেষে। অস্ট্রিয়ায় বসবাসকারী জার্মানদের ব্যাপার হল তারা বিপ্লবের মূল উৎপত্তির কারণটাকেই হয়ত বা ভুল বুঝেছিল; অথবা প্রথমদিকে ব্যাপারটাকে ঠিক মত বুঝে উঠতে না পারায় শেষমেষ তাদের ভাগ্যের দরজাটাই বন্ধ হয়ে যায়। এভাবে একরকম নিজেদের অজ্ঞাতসারে তারা। পশ্চিমের গণতন্ত্রে জাগরণ নিয়ে আসে এবং কালে যা তাদের নিজেদের অস্তিত্বটাকেই বিপন্ন করে তোলে।
এ তথাকথিত ব্যাপারটা দুঃখজনক হলেও অভিজ্ঞতা যে বাড়ায় তাতে সন্দেহ নেই। সহস্র ধারায় প্রবাহিত হয় এ অমোঘ ইতিহাসের আদেশ। এ বিশাল জনতার অন্ধত্ব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়ে অস্ট্রিয়ার ধ্বংস ডেকে আনে।
এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজনও যেমন নেই, অবকাশও কম। কারণ তা এ বইয়ের বিষয় বস্তুর বাইরে। আমি শুধু সে বিষয়গুলোর ওপরেই আলোকপাত করতে চাই, যেগুলো একটা জাতি এবং প্রদেশগুলোকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে গেছে। উপরন্তু এসব ঘটনাগুলো আমার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি বুঝতেও অনেক সাহায্য করেছে।
এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে যা সবচেয়ে বেশি ধ্বংস ডেকে এনেছে তা হল দুর্বল এবং সঙ্কীর্ণময় ব্যক্তিবর্গ, যারা নিয়মিত ভিড় করেছে পার্লামেন্টে বা ইপিরিয়াল কোর্ট-এ, অস্ট্রিয়ায় যে নামে পার্লামেন্টকে অভিহিত করা হয়।
এ ধরনের সম্মিলিত সভা ঠিক ইংল্যাণ্ডের অনুকরণে গঠিত হয়েছিল; ইংল্যান্ড হল গণতন্ত্রের স্বর্গভূমি।
প্রায় সময় সংঘটাই বলতে গেলে অস্ট্রিয়াতে পাচার করে দেওয়া হয়েছিল। সামান্য কিছু রদবদল করে।
ব্রিটেনের বদলী ভিয়েনাতে দু’কামরা বিশিষ্ট গণতন্ত্রের প্রচলন করা হয়। সহকারী সদস্যদের জন্য একটা কামরা আর লর্ডদের জন্য আরেকটা। বাড়িগুলোই অন্যরকম ঢঙে তৈরি করা হয়েছিল। ব্যারি যখন তার রাজপ্রাসাদ তৈরি করে, যাকে আমরা হাউস অফ পার্লামেন্ট বলে থাকি, টেমস নদীর ধারে, সে বাড়িটার স্থাপত্যের উৎসমুখ ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাস। সেই ইতিহাসের মধ্য থেকেই সে প্রচুর উপকরণ এবং মালমশলা সংগ্রহ করে যা দিয়ে ব্যারী বারশ’ কুলাচ্ছি, থাম প্রভৃতির অলংকরণ করে সেই রূপকথার মত সুন্দর প্রাসাদ ও অট্টালিকা তৈরি করে। সে অট্টালিকার গাম্ভীর্য এবং অলংকরণ, রঙ সবকিছুই জাতির জন্য একটা বিশিষ্ট মর্যাদার স্থান অধিকার করে। যেটা মন্দিরের মত পবিত্রও বটে।
এখানেই ভিয়েনা প্রথম অসুবিধার সম্মুখীন হয়। যখন হানসন, ওলন্দাজ স্থাপত্যবিদ সেই মর্মর প্রস্তরে তৈরি প্রাসাদটার ঢালু ছাদ দিয়ে ঘেরা দেওয়ালের তিন কোণা উপরিভাগ প্রায় শেষ করে এনেছে, ঠিক তখনই প্রয়োজন হয়ে পড়ে প্রাসাদটি অলংকরণের। কারণ এমন একদিন আসবে যখন সেইসব প্রতিনিধি নিয়মিত বসবে যারা সমস্ত দেশে জনপ্রিয়। সুতরাং অলংকরণের প্রয়োজনে তাকে বাধ্য হয়েই পুরনো দিনের মহৎ শিল্পের দিকে মুখ ঘুরাতে হয়। পশ্চিমী গণতন্ত্রের এ নাটকীয় মন্দিরকে সাজানো হয় বিভিন্ন মূর্তি দিয়ে। গ্রীক ও রোমান রাষ্ট্রনেতা ও দার্শনিকদের প্রতিচ্ছবি সে প্রাসাদে স্থাপন করে। যেন ভাগ্যের পরিহাসের মত, একদল উত্তেজক ঘোড়া পরস্পরকে টানছে ঢালু ছাদ দিয়ে ঘেরা চারিদিকের প্রাসাদটার দেওয়ালের দিকে। অবশ্য বাড়িটার ভেতরে যা চলছিল, এর থেকে ভাল প্রতীক অন্তত এ প্রাসাদে ব্যবহার করা সম্ভব ছিল না।
বাড়িটা অলংকরণের ব্যাপারে জাতীয়তাবাদীকে পুরোপুরি বর্জন করা হয়, ধরে নেওয়া হয়েছিল যে জাতীয়তাবাদী দোষের এবং তা জনসাধারণকে উত্তেজনার খোরাক। জোগাবে। এ একই ব্যাপার জার্মানিতে ঘটেছিল। রাইখষ্টা বাড়িটা যখন ভালেট তৈরি করে, তখন এটা জার্মান জাতির জন্য মোটেই তৈরি করা হয়নি; যতক্ষণ পর্যন্ত না বিশ্বযুদ্ধের কামান গর্জে ওঠে। তখন শুধু পাথরে খোদাই করা এক উৎসৰ্গনামা জনসাধারণের জন্য স্থাপন করা হয়েছিল।
আমার তখন কুড়ি বছর বয়সও হয়নি, যখন প্রথম সেই ফ্রাজেড্রিঙের প্রাসাদে সদস্যদের বক্তৃতা শোনার জন্য প্রবেশ করি। প্রথম অভিজ্ঞতাই প্রচণ্ড ঘৃণার উদ্রেক করে। সংসদকে আমি বরাবরই ঘৃণা করে এসেছি। তবে প্রতিষ্ঠান হিসেবে নয়, ঠিক তার উল্টো কারণে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা আস্বাদনের জন্য এর থেকে ভাল রাজনৈতিক পদ্ধতি আমি কল্পনাতেও আনতে পারি না। কিন্তু যে আলোর আশায় আমার হাবুসবুর্গ সংসদের পরিচয়, সে একনায়কতন্ত্রের কথা চিন্তা করার জন্য নিজেকেই অপরাধী বলে মনে হয়েছে।
অবশ্য আমার এ চিন্তাধারার পেছনে ব্রিটিশ সংসদের দান অনেকখানি। বয়সে কম ছিলাম বলে পত্র পত্রিকার মাধ্যমে সংসদের অতিরঞ্জিত করা ব্যাপার পড়ে আমার সংসদ রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ আরও বেড়ে যায় এবং এ আকর্ষণ আমি সে মুহূর্তে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারিনি। যেরকম অভিজাত্যের সঙ্গে ব্রিটিশ হাউস অ কমনস্ তাদের কর্তব্য সম্পাদন করত, তাতে আমার শ্রদ্ধা আর বেশি বেড়ে গিয়েছিল। এর জন্য অবশ্য অস্ট্রিয়ার সংবাদপত্রকে ধন্যবাদ, যারা গালভরা বিশ্লেষণ দিয়ে ঘটনাগুলোকে উপস্থাপিত করত। আমি নিজেকেই বারবার জিজ্ঞাসা করতাম, জনসাধারণের নিজস্ব দরকার ছাড়া অন্য কোন আর উন্নত ধরনের সরকার গঠন করা সম্ভব কিনা।
কিন্তু এ চিন্তাগুলোই আমাকে আরও বেশি অস্ট্রিয়ার পার্লামেন্টের বিরুদ্ধবাদী করে তোলে। যতদিন পর্যন্ত গোপন ভোটে নির্বাচনপ্রথা শুরু করা না হয়েছিল, ততদিন পর্যন্ত জার্মান প্রতিনিধিরাই সংখ্যায় বেশি ছিল। যদিও এ সংখ্যাধিক্য নামে মাত্র। এ পরিস্থিতিতে ব্যাপারটা আরও বেশি ঘোলাটে হয়ে ওঠে। কারণ জার্মানদের মধ্যে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের ওপর কখনই বিশ্বাস করা যায় না। বিশেষ করে জাতীয় বিপর্যয়ের সময়। জার্মানদের পক্ষে ব্যাপারটা আরও বেশি বিপদজ্জনক হয়ে উঠে, কারণ যে কোন বিষয়বস্তু আলোচনার সময়েই তারা জার্মানদের বিরোধিতা করতে শুরু করে। এর কারণ আর কিছুই নয়, তাদের ভয় অন্যান্য জাতীয়তাবাদী দলে তাদের যেসব অনুগত কর্মী আছে তারা যাতে দল ছেড়ে চলে না যায়। ভোট প্রথা চালু হওয়ার আগেই সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক দলকে তখন আর কোনক্রমেই জার্মান জাতীয়তাবাদী দল হিসেবে গণ্য করা চলে না। ভোটপ্রথা চালু করার সঙ্গে সঙ্গে জার্মান সংখ্যাধিক্যের পরিসমাপ্তি হয়। এভাবেই অস্ট্রিয়াতে জার্মানদের প্রভাব নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।
আমার জাতীয়তাবাদী মন এবং চরিত্র এ সদস্য ব্যবস্থাকে মেনে নিতে কখনই সায় দেয়নি, যাতে জার্মান জাতীয়তাবাদী দলকে সত্যিকারের প্রতিনিধিত্ব করতে দেওয়া হয়নি। কারণ যারা সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের এক অংশের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে, এরকম এবং আরও অনেক দোষ ত্রুটি, সেগুলোর জন্য পার্লামেন্টকে দোষারোপ করা ঠিক নয়। এরজন্য সম্পূর্ণ দায়ী অস্ট্রিয়া সরকার। এখন পর্যন্ত আমি বিশ্বাস করি যে যদিও জার্মান সংখ্যাধিক্য সংসদে পাওয়া যায়নি, তবু তার জন্য পার্লামেন্টারি প্রথাকে কোন রকমেই দোষারোপ করা চলে না। এরজন্য সম্পূর্ণ দায়ী তৎকালীন অস্ট্রিয়ার সরকার।
আমি যখন সে পবিত্র অথচ কলহমুখর সভায় প্রবেশ করি, তখন আমার ধ্যান ধারণা ছিল এরকম। আমার কাছে তার পবিত্র কারণ সেই গৌরবময় প্রাসাদের আনন্দব্যঞ্জক রূপ। জার্মানির মাটিতে একটা গ্রীক অত্যাশ্চর্যের নিদর্শন।
কিন্তু মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই সে বিকট দৃশ্য আমার চোখের ওপর ঘটতে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠি। কয়েক শ’সদস্য যারা একটা বিরাট অর্থনৈতিক সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য উপস্থিত এবং প্রত্যেকেই বক্তব্য রাখার জন্য উদগ্রীব।
আমার সে একদিনের অভিজ্ঞতা পরবর্তী অনেক সপ্তাহের ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করেছিল।
সে বিতর্কে বুদ্ধিমত্তার কোন ছাপই ছিল না। বরং তা অনেক নিচু গ্রামে বাধা। কখনও আমার মনেই হয়নি যে বিতর্করত সদস্যদের মাথায় কিছু আছে। বেশ কিছু সদস্য যারা সেখানে উপস্থিত, জার্মান ভাষাতেই তারা কথা বলেনি, শুধু সমানে নিজেদের প্রদেশের উপভাষা চালিয়ে গেছে। এভাবেই এতদিন যা সংবাদপত্রে পড়ে এসেছি মাত্র, তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করি। একদল অবাধ্য দাঙ্গাবাজ মানুষ বিশ্রী আকার ইঙ্গিত সহকারে হৈ হল্লা করে চলেছে, পরস্পরের প্রতি, আর করুণা পাওয়ার যোগ্য একজন বৃদ্ধ ক্রমাগত ঘন্টা বাজিয়ে সে হিংস্র সভার মর্যাদা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে; তার আবেদন, নিবেদন, উপদেশ বা পরামর্শ অথবা সতর্কতায় কেউ কান দিচ্ছে না।
ব্যাপার স্যাপার দেখে আমি না হেসে পারিনি। কয়েক সপ্তাহ পরে আবার আমি যাই। এবারের সভার চিত্র সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। এত আলাদা যে বোঝাই কষ্টকর এ সভাতেই আমি কয়েক সপ্তাহ আগে এসেছিলাম। পুরো সভাকক্ষই বলতে গেলে শূন্য। সংসদ সদস্যবৃন্দ নিচের আরেকটা ঘরে টানা ঘুম দিচ্ছে। মাত্র কয়েকজন সদস্য সভাকক্ষে পরস্পরের মুখোমুখি বসে আলস্য বিজড়িত হাই তুলছে। একজন সভাপতি চেয়ারে বসে। তার এদিক ওদিক তাকানোর ভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায় যে তার চেয়ারে বসে থাকতে একঘেঁয়ে লাগছে।
তখন পুরো ব্যাপারটা নিয়েই আমি গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করি। এবং সময় পেলেই আমি সংসদে যাওয়া শুরু করি নিঃশব্দে কিন্তু গভীর অভিনিবেশ সহকারে দর্শকদের লক্ষ্য করি। বিতর্ক শুনি এবং সেই মিশেলী রাজ্যগুলো থেকে আসা বিচিত্র সদস্যদের বুদ্ধির পরিমাপ করার চেষ্টা করি। ধীরে ধীরে আমার মনোজগতে একটা সুসংবদ্ধ চিন্তাধারা রূপ নেয়, যা যা দেখতাম তাকে অবলম্বন করে।
একটা বছর চুপচাপ পর্যবেক্ষণই আমার পুরনো ধ্যান-ধারণা ভেঙে সংসদের চরিত্র বোঝার পক্ষে যথেষ্ট। অস্ট্রিয়ার সংসদ সদস্যদের বিপথগামী সদস্যরা শুধু বিরোধিতা নয়, সমস্ত প্রথাটাকেই মেনে নেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। এতদিন পর্যন্ত ভেবে এসেছি যে অস্ট্রিয়ার সংসদের এ দুর্ভাগ্যজনক রক্তাল্পতার জন্য দায়ী জার্মান সদস্যদের লঘিষ্ঠতা। কিন্তু এখন বুঝতে পারি সংসদ গঠিতই হয়েছে ভুল উপাদানে।
তাদের জন্য অনেকগুলো সমস্যা এসে আমার মনের পর্দায় ভিড় করে। আমি ভোটদান পর্বটাকে নিয়ে অনেক চিন্তা করি আর সংসদ সদস্যদের বুদ্ধিমত্তা এবং নৈতিক দিকটার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও ভাবি।
সুতরাং এ পৃথিবীতে শুধু সংসদ চরিত্র নয়, যাদের দ্বারা এটা গঠিত তাদেরও অনুধাবন করতে পারি। এভাবে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে আমার সময়কার তথাকথিত পূজনীয় চরিত্র সম্পর্কে আমার মনের আয়নায় স্পষ্ট একটা ছবি ফুটে ওঠে, সে হল সংসদ সভাপতি। তার ছবিটা মনের এত গভীরে দাগ কেটে বসে যায় যে আজ পর্যন্ত তা ভুলিনি বা ভোলার প্রয়োজন হয়নি।
আরও একবার বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া এ সোজাসুজি শিক্ষা আমাকে ফাদে ফেলতে পারেনি, দিনের পর দিন লোককে প্রলুব্ধ করে এসেছে। যদিও পুরো ব্যাপারটাই হল মানব জাতির অবক্ষয়ের চিহ্নস্বরূপ।
গণতন্ত্র, যা আজকের পশ্চিম ইউরোপে মেনে চলা হয়, তা হল মার্কসীয় মতবাদের পথিকৃৎ। সত্যি বলতে কি মার্কসীয় মতবাদের জন্মই হয়েছিল গণতন্ত্রের গর্ভে। গণতন্ত্র হল মার্কসীয় বীজাণু জন্মনোর পক্ষে এক অতি উর্বর ক্ষেত্রবিশেষ, যাতে এ বীজাণু অতি দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পেতে পারে। আর এ সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রচলন হল অকালে গর্ভপাতের মত ঘটনা বিশেষ। যার শিক্ষা প্রচলিত হওয়ার আগেই সৃষ্টির আগুন নির্বাপিত।
আমি ভাগ্যের কাছে সত্যিই ঋণী যে ভিয়েনাতে থাকাকালীন ব্যাপারটা আমার নজরে এসেছিল। ঘটনাক্রমে যদি আমি জার্মানিতে থাকতাম, তবে হয়ত বা ব্যাপারটার ভাসা ভাসা একটা সমাধান খুঁজে পেতাম। আর যদি আমি বার্লিনে বাস করতাম তাহলে আমি প্রথমেই উপলব্ধি করতে পারতাম এ সংসদ কতখানি অযৌক্তিক, আমি হয়ত বা সহজেই অন্য প্রান্তে বিশ্বাস করতাম। যেরকম অনেকে কোন কারণ ছাড়াই বিশ্বাস করে যে জনসাধারণের রক্ষা পাওয়া সম্ভব যদি সাম্রাজ্যের ভিত দৃঢ় করা যায়, এবং সাম্রাজ্যের ভিত শক্ত করার একমাত্র পথ তথাকথিত রাজকীয় আদর্শগুলোকে সমর্থন করা। যারা এ পথে ভাবত, তাদের যেমন দূরদৃষ্টির অভাব ছিল, তেমনি জনসাধারণের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পর্কেও তারা অবহিত ছিল না।
অস্ট্রিয়াতে সহজে কাউকে প্রতারিত করা সম্ভব নয়। সেখানে একটা ভুলের মধ্য থেকে আরেকটা ভুলে পদক্ষেপ করা অসম্ভব। যদি সংসদ অর্থহীন হয়ে থাকে, তবে হাবুসবুর্গ নিকৃষ্টতম। অথবা বলা যায় সামান্যতমও ভাল ছিল না। কিন্তু সংসদীয় পদ্ধতিকে বাতিল করে দিয়ে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তক্ষুণ্ণি প্রশ্ন উঠতে পারে— তবে? তবে কি করা? ভিয়েনার সংসদকে বর্জন এবং ধ্বংস করে দিলে তো সমস্ত শক্তি গিয়ে জড় হবে হাবুসবুর্গের হাতে। আমার কাছে এ চিন্তাটা কল্পনায় আনাও সম্ভব ছিল না।
বিশেষ করে এ সমস্যাটা অস্ট্রিয়ার বেলায় এতই তীক্ষ্ম যে বাধ্য হয়েই সে অল্প বয়সে ব্যাপারটা নিয়ে অনেক বেশি মাথা ঘামাতে হয়, সমস্যাটা এত গভীর না হলে এটা আমি অন্তত সে বয়সে কখনই করতাম না।
পরিস্থিতি বিবেচনার পর যেটা প্রথমেই আমার নজরে পড়ে, সেটা হল সংসদ সদস্যদের ভেতর স্পষ্টত এককভাবে দায়িত্ব এড়িয়ে চলা।
সংসদের এক একটা আইন বা বিল পাশের প্রতিক্রিয়া দেশের চরম দুর্দশা ডেকে এনেছে। কিন্তু তার জন্য কাউকে দায়ী করা যায়নি। কোন একক ব্যক্তিকে কারণ দর্শাবার জন্য প্রশ্ন করাও সম্ভব নয়। কেউ হয়ত বলবে না যে সংসদ তার কর্তব্য সম্পাদন করেছে, যখন এসব আইন বা বিলের আনীত কোন দুর্যোগ উপস্থিত হওয়ার পর সভার কার্যকাল শেষ হয়ে যায়। অথবা সংসদ যখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাময়িক মিলনে গঠিত হয় বা ভেঙে যায়, তখনই কি সেই সংসদ তার ওপর সযত্নে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে? দায়িত্বের আদর্শ মানে কি একক ব্যক্তির ওপর অর্পিত দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া।
সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত নেতাদের, যারা জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত সদস্য বিশেষ কোন কার্যকলাপের জন্য তাদের কাছে কি হিসেব চাওয়া সম্ভব? নাকি, কোন নেতার পক্ষে এসব তথাকথিত নির্বোধ রাজনৈতিক ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কোন গঠনমূলক পরিকল্পনা পাওয়া যায়। তার পক্ষে এ ব্যবসায়ীদের তোষামোদ এবং অনুনয় বিনয় করেই সম্মতি আদায় করতে হয়।
এটাই কি একজন রাজনৈতিক নেতার পক্ষে অপরিহার্য গুণ যে, কোন একটা ভবিষ্যতের বীজকে বর্তমানের মাটিতে রোপণ করতে হলে তাকে সানুনয় বিনয় দ্বারা নিজের দৃষ্টিভঙ্গির সমানুপাতে সবাইকে নিয়ে আসতে হবে?
একজন রাষ্ট্রনেতা কি অযোগ্য বলে প্রমাণিত হবে যদি সে তার মতাদর্শ বেশির ভাগ ভোটে পাশ করতে না পারে?
অবশ্য বলা বাহুল্য সে সংসদ সদস্যদের বেশির ভাগ হয়ত বা জাল ভোটের দ্বারা নির্বাচিত।
এ সংসদ সভা কি কোনদিন কোন মুল্যবান রাজনৈতিক মতবাদ চালিয়ে তার মুল্য নিরূপণ করে তবে তা গ্রহণ করেছে?
বাস্তব পৃথিবীতে প্রতিভাবান ব্যক্তির প্রতিভা কি অলস এবং জড় জনতার দ্বারা সদাসর্বদা প্রতিহত হয়নি। তাহলে সে রাষ্ট্রনেতার কি করা কর্তব্য, যদি সে সেই দলে ভারী সংসদ সদস্যদের মতামত আদায় করতে না পারে? তবে কি তার কিছুর বিনিময়ে তা কেনা উচিত? অথবা যদি সে নেতা খোশামুদি করে একগুঁয়ে সদস্যদের সন্তুষ্ট করতে না পারে, তবে সে কি সেপথ ছেড়ে দেবে, যা সে জাতির প্রতি প্রয়োজনীয় এবং সঠিক বলে মনে করেছিল। এ অবস্থায় তার কি রাজনৈতিক জীবন থেকে অবসর নেওয়া উচিত? নাকি ক্ষমতায় থাকবে?
এরকম পরিস্থিতিতে সত্যিকারের চরিত্রবান একজন রাষ্ট্রনেতা কি তার নিজের মুখোমুখি হবে না? একদিকে তার নিজস্ব রাজনৈতিক চিন্তাধারা, অপরদিকে নৈতিক ন্যায়, নিষ্ঠা আরও স্পষ্টভাষায় বলতে গেলে নৈতিক সাধুতা।
তা হলে ঠিক কোথায় আমরা জনসাধারণের প্রতি কর্তব্য এবং নিজের সম্মানবোধের সীমারেখা টানব?
সত্যিকারের একজন নেতা নিশ্চয়ই তাকে ঠিকাদারের পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে আসার কথা চিন্তা করবে না। এবং অপরদিকে, প্রতিটি রাজনৈতিক ঠিকাদার কি ভাববে না যে সেও রাজনীতির এ খেলায় মাতে? কারণ ব্যক্তিগত কাউকে তো হিসেবের জন্য বলা যাবে না; তার দায় তো অগুস্তি জনসাধারণের।
সুতরাং নিশ্চিন্তরূপেই বলা যায় যে সংখ্যাধিক্য নির্বাচিত সংসদীয় এ গণতান্ত্রিক সরকার কি একজন রাষ্ট্রনেতার আদর্শকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে না?
সত্যিই কি কেউ বিশ্বাস করে যে মানুষের প্রগতি শুধুমাত্র একদল মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত? কোন একক ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা এবং সদিচ্ছা দ্বারা তা সম্ভব নয়? অথবা, এটাই ধরে নেওয়া যায় যে ভবিষ্যৎ মানবিক সভ্যতা এ পরিস্থিতিতেই শুধু বেঁচে থাকবে?
তবে কি আজকের মত সেদিন একক ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা এতটা নির্ভরশীল ছিল না?
সংসদীয় গণতন্ত্রে বিধান সম্বন্ধীয় ক্ষমতায় একক ব্যক্তির বুদ্ধিমত্তা খারিজ হয়ে যেত একদল বেনামী মাথার কাছে। কিন্তু এভাবে প্রকৃতির মূল আইন অর্থাৎ আভিজাত্যেই সংঘাত লাগত। যদিও এ অবক্ষয়ের যুগে আমাদের বোঝা উচিত এ আভিজাতপূর্ণ চিন্তাধারা শুধু সমাজের ওপরের স্তরের হাজার দশেক লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই।
যারা ইহুদী প্রেসের সঙ্গে পরিচিত, তাদের পক্ষে এ সংসদীয় ক্ষয়িত শক্তি সম্পর্কে কোনরকম আঁচ করা সম্ভব নয়। যদি না তারা নিজেরা নিজেদের ভেতরে স্বতন্ত্র চিন্তাধারা গড়ে তুলতে পারে, বা সংবাদগুলো যাচাই করার ক্ষমতা রাখে। এ প্রতিষ্ঠানগুলোই রাজনীতিতে অতি সাধারণ লোকেদের ভিড় বাড়ানোর জন্য দায়ী। এসব বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে একজন পুরুষ যার ভেতরে সত্যিকারের রাষ্ট্রনেতা হবার যোগ্যতা আছে, সে চেষ্টা করবে রাজনীতির প্রাঙ্গণ এড়িয়ে যেতে। কারণ এ পরিবেশে যার গঠনমূলক কাজ করার ক্ষমতা আছে, তা তাকে করতে দেবে না। বরং যার পক্ষে অধিকাংশের ভিড়ে ভিড়ে যাওয়া সম্ভব, রাজনীতি তাকেই আকর্ষণ করবে। সুতরাং এ পরিবেশ সংকীর্ণমনাদের জন্য এবং তাদেরই টানবে।
মানসিক দিক থেকে সংকীর্ণমনা এবং জ্ঞানের দিক থেকে অপ্রতুল এসব রাজনীতির দিনমজুরদের রাজনীতি সম্পর্কে জ্ঞানের ভান্ডার সীমাবদ্ধ, যার জন্য সে স্বভাবতই জনতার মনের ভিড়ে নিজের মতাদর্শ মিলিয়ে যেতে দেবে যাতে তার প্রতিভা বা বুদ্ধিমত্তার পরিমাপ কেউ করতে না পারে; বরং এ ধরনের কৌশলপূর্ণ বিচক্ষণতা একজন অভিজ্ঞ সরকারি কেরাণীর পক্ষে ভাল, কিন্তু একজন রাজনীতিজ্ঞের জীবনে নয়। বাস্তবিকপক্ষে তার ধ্যান ধারণা এ সংকীর্ণ কৌশল রাজনৈতিক প্রতিভার চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। এ ধরনের সাধারণ লোকে তার কাজ সম্পর্কে কোনরকম দায়িত্ব গ্রহণের উদ্বিগ্নতা থেকে মুক্ত। কারণ প্রথম থেকেই তার রাষ্ট্রনৈতিক খেলার ফলাফল যাই হোক না, পরমায়ু তো তারার আলোর মত বাঁধাধরা। একদিন তারই মত বুদ্ধিসম্পন্নকে তার জায়গাটা ছেড়ে দিতে হবে। আমাদের এ ক্ষয়িত যুগে এ কারণেই সম্ভবত উচ্চ ধীশক্তিসম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞের অভাব ঘটেছে। এবং যত বেশি একক ব্যক্তিত্ব সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে, তত বেশি এ ক্ষমতা কমে আসবে। সত্যিকারের রাজনৈতিক প্রতিভাসম্পন্ন কেউ এ ধরনের হাঁসের ঝাঁকের ভিড়ে উচ্চ কণ্ঠস্বরে দি দিগন্ত নিনাদিত করবে না।
আর এ ধরনের সভাপতিদের একমাত্র সান্ত্বনা যে যেসব সদস্যদের তাকে পরিচালিত করতে হয়, তাদের বুদ্ধিমত্তাও তার চেয়ে বেশি নয়। সুতরাং সবাই একই ধরনের বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন হওয়ায় বিতর্ককালে ভাবে যে এমন একদিন আসবে যখন অপরকে ডিঙিয়ে তার পক্ষে ওপরে ওঠা সম্ভব। আজকে যদি পিটার কর্তা হতে পারে, তবে আগামীকাল পাউলারই বা তা হতে বাধাটা কোথায়? বুদ্ধির ব্যারোমিটারের পারা যখন উভয়েরই একসুরে বাঁধা।
এ নয়া গণতন্ত্রের একটা অদ্ভুত দিক আছে, যেটা প্রচণ্ড রকমের অপকার ছড়ায় সমাজে। সেটা হল আমাদের বিরাট একদল তথাকথিত রাজনৈতিক নেতা উৎপাদন। যখনই কোন জরুরী বিষয়ের অবতারণা করা হয়, তারা তক্ষুণ্ণি সংখ্যাধিক্যের পেছনে মুখ লুকায়।
এসব রাজনৈতিক কৌশলগুলো একটু মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে কিভাবে মিষ্টি কথায় সংখ্যাধিক্য সদস্যদের ভুলিয়ে ভালিয়ে সে যা করতে চায় তার মতামত আদায় করে নিচ্ছে। আর এসবই হল মূল কারণ যার জন্য সাহসী এবং চরিত্রবান কোন রাজনৈতিক নেতার কাছে পুরো ব্যাপারটাই ঘৃণ্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিচুস্তরের লোকদের ঠিক এ জিনিসটাই প্রচন্ড আকর্ষণ করে, যারা নিজেদের কাজকর্মের দায়িত্ব নিতে অনিচ্ছুক, কিন্তু সব সময়ই নিজেদের কৃতকর্মের জন্য একটা আবরণ খুঁজে বেড়ায়। তাদের বদমাস এবং অসৎ লোকদের দলে দেখা উচিত। যদি কোন জাতীয় নেতা রাজনীতির নিচুস্তরের থেকে আসে, তবে তার মধ্যেও এসব দুষ্ট কৌশল প্রবেশ করবে। কারও পক্ষেই তখন সাহসের সঙ্গে কোন নির্দিষ্ট পথ নেওয়া সম্ভব নয়। তারা তখন গালাগাল এবং অখ্যাতির কাছে নতি স্বীকার করে নিয়ে সাহসের সঙ্গে কোন মত প্রকাশ করবে না। এভাবে একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না যে তার ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানকে বাঁধা রেখে রাজনীতির নির্দিষ্ট পথে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে প্রয়াসী।
একটা সত্য সবসময় মনে রাখা উচিত যে সংখ্যাধিক্য কখন একক ব্যক্তিত্বের পরিপূরক হতে পারে না। সংখ্যাধিক্য শুধু অজ্ঞতাই প্রকাশ করে না, কাপুরুষও হয় বটে। যেহেতু একশো বোকা একজন জ্ঞানীর সমতুল্য নয়, সেই রকম একজন কষ্টসহিষ্ণু এবং নৈতিক চরিত্রবান রাজনীতিজ্ঞের পক্ষে রাজনীতির ক্ষেত্রে যা করা সম্ভব, একশোটা কাপুরুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়।
কর্তব্যের বোঝা একজন নেতৃত্বের ওপর যত কম চাপবে, ততবেশি উটকো সাধারণ নেতার দল তাদের দুর্নীতির বোঝা কমাতে জাতির কাছে ভিড় জমাবে। তারা উচ্চাকাঙ্ক্ষার এত বেশি উঁচু শিখরে অবস্থান করে যে তাদের পক্ষে তাদের জন্য নির্দিষ্ট এবং যথাযথ সময়ের জন্য অপেক্ষা করতে পারে না। লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে তাদের সামনের অপেক্ষাকৃত লোকগুলোকে বিষন্ন মুখে গোনে এবং মনে মনে নির্দিষ্ট প্রহরের আঁক কষে কখন তাদের পালা আসবে। তারা প্রতিটি ঘটে চলা ঘটনাকে পর্যবেক্ষণ করে
যা তাদের প্রতিনিয়ত আশা নিরাশায় দোল দেয় এবং প্রত্যেকটি অপবাদকে উপভোগ করে, যা লাইনে দাঁড়ানো অন্য প্রার্থীদের লাইন থেকে সরিয়ে দিয়ে তাকে ইঙ্গিত বস্তুর প্রতি এগিয়ে দেবে। যদি কেউ ভাগ্যক্রমে দীর্ঘদিন তার চেয়ার দখল করে বসে থাকে, তবে তারা এটাকে তাদের প্রতি পরস্পরের বোঝাপড়ার বিশ্বাসঘাতকতা বলে ধরে নেয়। তারা এত হিংস্র হয়ে ওঠে যে যতক্ষণ পর্যন্ত না সেই দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকটা আরামপ্রদ জনসাধারণের দেওয়া গদি না ছাড়ে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা কিছুতেই শান্ত হয় না। অবশ্য এ ধরনের ঘটনার পর তার আবার সেই গদীতে ফিরে আসার সম্ভাবনা খুব কমই থাকে। সাধারণত তাড়িয়ে দেওয়া এ লোকগুলো আবার গিয়ে লাইনে ভিড় করে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত লাইনের দাঁড়ানো অন্যান্য উচ্চাকাক্ষীর দল এদের তাড়িয়ে দেয়।
সরকারি পরিচলন ব্যবস্থায় এ ধরনের হঠাৎ পরিবর্তনের ফলে অনেক সময়েই গণজীবনে বিপর্যয় নেমে আসে; বিশেষত দেশ যখন কোন কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি। শুধু অজ্ঞ এবং অযোগ্য ব্যক্তিরাই এ সংসদীয় গণতন্ত্রের বলি হয় না। সত্যিকারের যোগ্য নেতৃত্বও অনেক সময় এ পরিস্থিতির শিকার হয়ে পড়ে, যদি না ভাগ্য তাকে যোগ্য হওয়াতে নেতার পদে ঠেলে দেয়। আর যখনই তার যোগ্যতার আভাস ফুটে ওঠে, তখন অযোগ্যরা দল বেঁধে তার বিরুদ্ধাচারণ করতে নামে। বিশেষ করে যদি সে নেতা তাদের দল থেকে না আসে এবং তথাকথিত ঝলমলে এ দুর্বল চিত্ত লোকদের সঙ্গে তার মেলামেশার অভ্যাস না থাকে। তারা স্বভাবত তাদের নিজেদের যুথের মধ্যেই ঘোরাফেরা করে এবং কেউ যদি তাদের সমকক্ষ হয়, তৎক্ষণাৎ তারা দল বেঁধে তার বিরুদ্ধচারণ করে। তাদের সহজাত প্রকৃতি অন্যদিকে ভোতা হলেও এ বিষয়ে অত্যন্ত প্রখর।
এর অবশ্যম্ভাবী ফলাফল হল সরকারি পরিচালন ব্যবস্থায় বুদ্ধিমানের দল ক্রমাগত আর বেশি করে ঢোকে। যদি কেউ এ শ্রেণীর নেতা না হয়, তবে তার পক্ষে ভবিষ্যদ্বাণী করা অতি সহজ যে এ পরিস্থিতিতে একটা জাতি এবং দেশের কতটা ক্ষতি হতে পারে।
পুরনো অস্ট্রিয়ার সংসদীয় গণতন্ত্র মূল আদর্শের দিক থেকে হুবহু একই রকম ছিল, যার বর্ণনা আমি ওপরে দিয়েছি।
যদিও অস্ট্রিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হত সম্রাটের দ্বারা, তবু এ নিযুক্ততা সত্যিকারের সংসদীয় কার্যকলাপে কোন ঢেউ তুলতে পারত না। ফেরিওয়ালা মনোবৃত্তি আর দর কষাকষি এ সব মন্ত্রীত্ব পদ নিয়ে এত বেশি চলত যে পশ্চিমী গণতন্ত্রের সত্যিকারের রূপ এর মাধ্যমেই ফুটে উঠত। আদর্শ অনুযায়ী ফলাফলও প্রকাশিত হত; দুজনের ভেতর বদলির সময় কমতে কমতে এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়ায় যে তাকে পরস্পরের প্রতি মৃগয়া ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। প্রতিটি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নেতার গুণাবলী কমতে বাধ্য; শেষপর্যন্ত সে ছোট্ট ধরনের রাজনৈতিক ফেরিওয়ালায় পরিণত হয়। এসব লোকের ক্ষেত্রে নেতৃত্বের পরিমাপ হল— কত নিপুণতার সঙ্গে মিশ্রিত রাজনৈতিক দলগুলোকে সে টুকরো টুকরো করতে পারে। অন্য কথায় বলা যায়, এদের কৌশল হল ননাংরা রাজনৈতিক পট পরিবর্তন; আর সেটাই হল এ ধরনের সদস্যদের সত্যিকারের যোগ্যতর কাজ।
এ ব্যাপারে ভিয়েনাকে একটা শিক্ষায়তন বলে অভিহিত করা চলে, যার যোগ্য উদাহরণ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া মুস্কিল।
আর একটা ব্যাপার, যেটা আমার সব সময় নজরে আসত সেটা হল তার চারিত্রিক বিরোধিতা; জ্ঞান এবং প্রতিভার দিক থেকে শুধু যে একের সঙ্গে অপরের কোন মিলই নেই শুধু তা নয়, প্রকৃতিগত ভাবেও এরা পরস্পর বিরোধী। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এসব বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে উদ্ভূত সদস্যদের সংকীর্ণতার চিন্তা থেকে কেউ মুক্ত হতে পারত না। তারা একরকম বাধ্য হয়ে ভাবত কিভাবে এ তথাকথিত মহান চরিত্রগুলো প্রথম গণমানসে উদিত হল।
এটা সত্যি একটা গবেষণার বিষয় যে এসব ভণ্ড ব্যক্তিরা তাদের প্রতিভাকে কিভাবে দেশের কাজে লাগাত। স্পষ্টভাবে বলতে গেলে, ওদের কার্যপ্রণালীর বিস্তারিত খোঁজখবর নেওয়া অত্যন্ত জরুরী।
সংসদীয় গণতন্ত্রের জীবনটা যত বেশি স্পষ্ট করে ধরা দেয়, মানুষের আশাও তত বেশি নিভে আসে। বিশেষ করে যখন কেউ এর সত্যিকারের চেহারা এবং যাদের নিয়ে এটা গঠিত তা বিশেষভাবে অনুধাবন করে। অবাক হতে হয় এ সংসদীয় গণতন্ত্রের আদর্শগত কাৰ্যসূচীর দিকটার দিকে নজর দিলে। সত্যি বলতে কি, এর বৈষয়িক দিকটাকে ভালভাবে বোঝা উচিত, কারণ এসব প্রতিষ্ঠানের ধর্মপিতার দল প্রতি কথায় এর বৈষয়িক দিকটাকেই জনসাধারণের চোখে তুলে ধরতে সচেষ্ট থাকে। তাদের কথায় তো মনে হয় পুরো ব্যাপারটাই পরিষ্কার পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং ন্যায় বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু কেউ যদি এসব ভদ্রলোকদের এবং তাদের অতি অধ্যাবসায়ে তৈরি আইন-কানুন সতর্কভাবে পরীক্ষা করে দেখে, তবে তার ফলাফল দেখে অবাক হয়ে যাবে।
সংসদীয় গণতন্ত্রের আদর্শের মত এত অন্তঃসারশূন্য আর কোন আদর্শকে সম্ভবত খুঁজে পাওয়া যাবে না। যদি অবশ্য এর বৈষয়িক দিকটা বিচার করা যায়।
আমাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রথম ধাপে কিভাবে নির্বাচন পর্ব সমাধা করা হয়, সেটা বিচার করবে। তার সঙ্গে সঙ্গে এটাও দেখা উচিত যে তারা কিভাবে অফিসে আসে এবং নতুন নামে অর্থাৎ সংসদ সদস্য হিসেবে নিজেদের চেয়ারে স্থাপন করে। এটা সত্য যে মাত্র অল্পসংখ্যক জনসাধারণের ইচ্ছা বা প্রয়োজনই মাত্র এ তথাকথিত গণতান্ত্রিক নির্বাচনে প্রতিফলিত। প্রত্যেকে, যাদের কিছুটা রাজনৈতিক চেতনা আছে এবং জনসাধারণের রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার দিকটা বোঝে, তারা সবাই জানে যে সাধারণ জনগণের রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি অত্যন্ত কম, তাই তাদের পক্ষে এমন কাউকে নির্বাচন করাও সম্ভব নয় যে তাদের চিন্তাধারাকে রূপ দিতে সক্ষম।
আমরা যতই বলি না কেন ‘গণ মতামত’ কিন্তু বাস্তবে অতি অল্প সংখ্যক লোকের চিন্তাধারা এবং অভিজ্ঞতা প্রসূত হল এ মতামত। এর বেশির ভাগ ফলাফলই আসে জনসাধারণের কাছে ফুলিয়ে ফঁাপিয়ে নিপুণভাবে পরিবেশিত হয়ে।
ধর্মের জগতে সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস আসে শিক্ষার দিক থেকে। কিন্তু ধর্মের বার্ধক্যহেতু তা অলসভাবে মাটির ওপর ঘুমিয়ে থাকে। আর সেই কারণেই জনসাধারণের রাজনৈতিক মতামত গড়ে ওঠে মানুষের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে সুড়সুড়ি ও বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগে অবিশ্বাস্য ধৈর্য প্রয়াসের ফলে।
রাজনৈতিক শিক্ষার সবচেয়ে ফলপ্রদ দিক হল সংবাদপত্রের ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে সংবাদ পরিবেশনার দিকটা। সংবাদপত্রই হল রাজনৈতিক আলোকসম্পাতের প্রধানতম হাতিয়ার। এটা প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য এক রকমের স্কুলও বলা চলে। এ শিক্ষা কর্মকাণ্ডটি সরকারের হাতে থাকে না। এটা থাকে তাদের হাতে চরিত্রের দিক থেকে যারা অতি নিম্নস্তরের। যৌবনকালে ভিয়েনায় থাকাকালীন এসব মানুষের সংস্পর্শে আসার সুযোগ হয়েছিল, যাদের হাতে এ লোকশিক্ষার যন্ত্র, তাদের মাধ্যমে এর আদর্শও জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হতো। প্রথমে তো আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। কত ক্ষুদ্র সময়ে এ ভয়ঙ্কর শক্তিধরটি জনসাধারণের মধ্যে কোন বিশেষ একটা বিশ্বাস উৎপাদন করতে সক্ষম। এবং তা, এ পথে চলতে গিয়ে প্রায়ই জনসাধারণের ইচ্ছা ও মতবাদকে উপস্থাপনা করে। একটা হাস্যাস্পদ তুচ্ছ ঘটনাকে জাতীয় পর্যায়ে তুলে আনতে সংবাদপত্রের মাত্র কয়েকদিন সময়ের প্রয়োজন হয়। যে মাধ্যমে জাতির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কোন একটা সমস্যাকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা, অপহরণ বা অন্য কোন উপায়ে জনসাধারণের কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে লুকিয়ে রাখে।
সংবাদপত্রের আর একটা ভাণুমতীর খেলা হল কোথা থেকে একটা নাম খুঁজে পেতে বার করে এনে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলা। আগে হয়ত কেউ সে নাম শোনেনি। তারা নামগুলোকে এমনভাবে জনসাধারণের কাছে উপস্থাপিত করে যেন সেই নামগুলোর সঙ্গে জনসাধারণের অনেক আশা জড়িয়ে আছে। তারা নামটাকে জনপ্রিয়তার এতটা উঁচু ধাপে টেনে তোলে যা সত্যিকারের কোন ক্ষমতাসম্পন্ন নেতার পক্ষে সারাজীবনেও সেই জনপ্রিয়তা অর্জন করা সম্ভব নয়। এ সমস্ত করা হয়, যদিও এ সব নামগুলো হয়ত বা মাসখানেক আগেও অশ্রুত ছিল এবং কেউ উচ্চারণ পর্যন্ত করত কিনা সন্দেহ, সংবাদপত্র এগুলোকে খ্যাতির পাহাড়ের চূড়ায় টেনে তোলার আগে। সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন এবং ক্লান্ত রাজনৈতিক জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠিত লোকদের নাম এ সংবাদপত্রগুলো জনসাধারণের স্মৃতিশক্তি থেকে ধীরে ধীরে আবছা করে এনে শেষে একসময় ভুলিয়ে দেয়, যেন তারা মৃত। যদিও তখন তারা অনেক স্বাস্থ্যবান এবং পরিপুর্ণ উৎসাহে টগবগ করে ফুটছে। অথবা, অনেক সময় এসব লোকদের প্রতি এমন সব ননাংরা গালাগাল বর্ষণ করা হয় যে জনসাধারণের মনে করে এরা অত্যন্ত নিচ। সংবাদপত্রের অনিষ্ট করার ক্ষমতা যে কত দূর; সঠিকভাবে বুঝতে হলে বিশেষ করে কুখ্যাত ইহুদী সংবাদপত্রগুলোকে অনুধাবন করা উচিৎ। সে কুখ্যাত ইহুদী সংবাদ পত্রগুলোর সংবাদ পরিবেশনা করার পদ্ধতি দ্বারা তারা সম্মানিত এবং সুন্দর লোকগুলোর নাম প্রথমে জনসাধারণের স্মৃতিতে মলিন করে আনে। তারপর তার প্রতি এমন খিস্তি খেউরের কাদা ছেড়ে চারদিক থেকে যে পুরো ব্যাপারটাই যাদুর মত কাজ করে।
এ তথাকথিত ডাকাতের দল তাদের শয়তানের চক্র সফল করার জন্য কিছু করতেই দ্বিধা করে না।
তারা এমন কি পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলিয়ে এমন কয়েকটা নোংরা ব্যাপার নিয়ে কাদা ছোড়াছুড়ি করে যাতে প্রতিপক্ষের সম্মান সম্পূর্ণভাবে ধূলোয় লুটিয়ে পড়ে। কিন্তু এসব না নামান যায়, তখন এরা তাকে লক্ষ্য করে কুৎসিত গালাগাল দেয় এ বিশ্বাসে যে তার কিছু অংশ প্রতিপক্ষের গায়ে লেগে থেকে জনসাধারণের কাছে তাকে হেয় করে তুলবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একে প্রতিরোধ করার কোন অস্ত্র প্রতিপক্ষের হাতে আর থাকে না। কারণ এরা একসঙ্গে এতগুলো কৌশল অবলম্বন করে যে তা দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকে। কিন্তু বাইরে থেকে এতটুকু বোঝার উপায় নেই যে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এগুলো করা হচ্ছে। জনসাধারণও তা বুঝতে পারে না। যেসব শয়তানের দল তার সমকালীন কাউকে এরকম অপমানকরভাবে নিচে নামায় এবং নিজেরা নায়ক সেজে যশের মুকুট মাথায় পরে, সেইসব দুবৃত্তদের সাংবাদিকতার কর্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে দেখা যাবে তৈলযুক্ত কথায় নির্বাচিত সেকেল বোকা বোকা শব্দ দ্বারা তারা নিজেদের জয়টাক পিটাচ্ছে। যখন এ খুঁটে খাওয়া মাছগুলো এক জায়গায় মাছের ঝাঁকে জড় হয় এবং সেই সভায় তারা এঁটেল মাটির মত সেঁটে বসে তাদের নিজেদের সম্মানের কথা বলে চলে যাকে তারা বলে সংবাদপত্রসেবীদের সম্মানে সম্মানিত ব্যক্তি। তখন আবার তারা পরস্পরকে উচ্চতর জীব ভেবে নিয়ে মাথা বঁকিয়ে সম্মানও জানায়।
এ জঘন্য প্রকৃতির জীবেরাই তথাকথিত জনসাধারণের মতামত নিজেদের কল্পনায় তৈরি করে।
পদ্ধতিটার পুরোপুরি হিসেব এবং তার ভ্রমাত্মক ধ্যান-ধারণার শূন্যগর্ভ সম্পর্কে বলতে গেলে বেশ কয়েক অধ্যায়েও কুলাবে না। সুতরাং এ ব্যাপারে বিস্তারে না গিয়ে এর কাজ চলাকালীন ফলাফল বিচার করব এবং আমি মনে করি নির্দোষ এবং সরল বিশ্বাসী লোকেদের জ্ঞানচক্ষু খুলে দেওয়ার পক্ষে এটাই যথেষ্ট। ফলে তারা এ প্রতিষ্ঠানের বৈষয়িক দিকটার অসারত্ব সম্পর্কে সহজেই বুঝতে পারে।
এ গণমানসের নৈতিক অবনতি কতখানি ক্ষতিকারক, যা বোঝার সবচেয়ে সহজ এবং সর্বোত্তম উপায় হল এ সংসদীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে যদি জার্মান গণতন্ত্রের কেউ তুলনা করে।
এ সংসদীয় গণতন্ত্রের সবচেয়ে বিস্ময়কর দিকটা হল একদল লোক, ধরা যাক বর্তমানে শ’ পাচেক তার মধ্যে স্ত্রীলোকও আছে, সংসদে নির্বাচিত হয়ে আসে। তারপর যে কোন বিষয়ে অর্থাৎ সব বিষয়েই তাদের ওপর শেষ বিচারের পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হয়। প্রকৃতপক্ষে তারাই কিন্তু সবকিছুর পরিচালক, যদিও তারা নামে একটা মন্ত্রীসভা গঠন করে এবং বাইরে থেকে মনে হয় এ মন্ত্রীসভাই বুঝি সবকিছু চালনা করছে। কিন্তু সত্যিকারের খতিয়ে দেখতে গেলে মন্ত্রীসভার আলাদা কোন অস্তিত্ব নেই। আসলে সংসদ সদস্যদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সরকারের কিছু করার ক্ষমতাই নেই। এমন কি কোন একটা বিষয়ের হিসেব নিকেশও পাওয়া এদের কাছ থেকে অসম্ভব। কারণ করণীয় কিছু করার দায়িত্ব তো তথাকথিত মন্ত্রীসভার নয়; সংসদের অধিকাংশ সভ্যের ভোটে তা ঠিক করা হয়েছিল। সংসদের গরিষ্ঠ সদস্যদের চিন্তাধারার বাহন হল মন্ত্রীসভা। এর রাজনৈতিক সফলতা নির্ভর করে কতটা পরিমাণে এরা গরিষ্ঠ সদস্যদের সঙ্গে নিজের মত মিলিয়ে নিয়ে মানিয়ে থাকতে পারে। অথবা পড়িয়ে উড়িয়ে তাদের নিজেদের মতামত গ্রহণ করতে বাধ্য করে। কিন্তু এর অর্থ হল সত্যিকারের শাসকের আসন থেকে নিচে নেমে ভিক্ষাজীবিদের ন্যায় গরিষ্ঠ সংসদ সদস্যদের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি করে মত আদায় করা। সত্যি বলতে কি মন্ত্রীসভার প্রধান কাজই হয়ে দাঁড়ায় শেষ পর্যন্ত শাসকদলের গরিষ্ঠ সদস্যদের নিজেদের পক্ষে দলে টানা। আর টানতে না পারলে নতুন গরিষ্ঠতা অর্জনে সচেষ্ট হওয়া। যদি দু’য়ের মধ্যে একটাতেও এরা সাফল্য লাভ করতে পারে, তবেই সরকারে এরা টিকে থাকে। আর গরিষ্ঠ সদস্যদের মতামত নিজেদের স্বপক্ষে জড় করতে না পারলে স্বভাবত মন্ত্রীসভাও ভেঙে যায়।
কিন্তু এ দুই প্রচেষ্টার একটাও যদি সাফল্য লাভ করতে পারে, তবে আর কিছুদিনের জন্য মন্ত্রীত্ব চালিয়ে যেতে পারে। এখন প্রশ্ন হল, এ ধরনের রাজনীতি সঠিক না বে ঠিক? অবশ্য এর কোন অর্থ নেই। দুটোর মধ্যে যেটাই হোক না কেন?
এভাবেই বাস্তবে সবার দায়িত্ব ধুয়ে মুছে যায়। তবে এর ফলাফল একটা রাজ্যকে কোথায় টেনে নামাতে পারে সেটা বোঝার জন্য নিম্নবর্ণিত সহজ ঘটনাপঞ্জী পড়লেই বোঝা সম্ভব।
এ পাঁচশ সদস্য, যারা জনসাধারণের ভোটে সংসদে নির্বাচিত, তারা আসে জীবনের অসমতল ক্ষেত্র থেকে। সুতরাং তাদের মধ্যে পারস্পরিক রাজনৈতিক ক্ষমতাতেও যে মিল থাকবে না তাতে আর আশ্চর্য কি। যার ফলে সেগুলোকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগের সময় প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় এবং সমস্ত ভবিষ্যতের ছবিটাই বিবর্ণ হয়ে আসে। এটা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে যদি কেউ চিন্তা করে এ নির্বাচিত পাঁচশ প্রতিনিধি হল উৎসাহ এবং বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ তাহলে সেটা মস্ত ভুল। এমন নির্বোধ সম্ভবত একজনকেও পাওয়া যাবে না যে নাকি ভাবে যে এ তথাকথিত ভোটের কাগজগুলো থেকে হঠাৎ শয়ে শয়ে রাষ্ট্রনেতা বেরিয়ে আসবে; যারা আর যাই হোক সাধারণের চেয়ে একবিন্দুও বুদ্ধি বেশি রাখে না। প্রতিভাবানরা যেসব ধ্যান ধারণা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, এক কথায় তা নাকচ করে দেওয়া সম্ভব নয়। বরং সত্যিকারের একজন রাষ্ট্রনেতার অভ্যুদয় একটা জাতির পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ। কারণ এসব রাষ্ট্রনেতারা ঝাঁকে ঝকে আসে না। দ্বিতীয়ত, জনসাধারণের প্রতি একটা স্বাভাবিক অনীহা ভাব থাকে। ভোটের দ্বারা নির্বাচিত সত্যিকারের একজন রাষ্ট্রনেতার সন্ধান পাওয়ার চেয়ে সম্ভবত একটা ছুঁচের সুতো গলার ফাঁক দিয়ে পুরো একটা উট গলে যাওয়াও সহজ।
ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে জনসাধারণের যা অতীতে উপকার করেছে, তা সম্ভব হয়েছে একক কোন ব্যক্তির উৎসাহ এবং কর্মশক্তির তৎপরতায়।
কিন্তু গণতন্ত্রের দোহাই পড়ে এখানে পাঁচশ অতি সাধারণ বুদ্ধিজীবি মানুষ জাতির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সমস্যা নিয়ে বিচার করে তার রায় দেয়। তারা যে সরকার তৈরি করে প্রতিটি ক্ষেত্রে সেই মন্ত্রীসভাকে সেই রঙচঙে সংসদের অনুমোদন নিতে হয়, অর্থাৎ যে পথ তারা বাছে, সেটা হল পাঁচশ লোকের মিলিত পথ।
যাহোক, এসব সদস্যদের বুদ্ধিমত্তার দিকটার দিকে যদি আলোকপাত করা যায় তবে দেখা যাবে কি ধরনের কাজকর্ম এসব পদের জন্য অপেক্ষা করছে। যদি আমরা এসব সমস্যার সত্যিকারের রূপটা চিন্তা করি, তবে দেখতে পাব, কত রকমারি এবং বিভিন্ন রকম। সদস্যগুলোর ধরন। তখনই বুঝতে কষ্ট হয় না যে তথাকথিত মন্ত্রীসভা এসব নানামুখী সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে কতখানি অজ্ঞ। একে তো তাদের মধ্যে বুদ্ধিমত্তার অভাব, তদুপরি অভিজ্ঞতা বলতেও কিছু নেই, সুতরাং সমস্যাগুলোর সমাধান কি করে করবে? একটা অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য যখন সংসদে উপস্থিত করা হয়, তখন দেখা যাবে যে এক দশমাংশ সদস্যেরও প্রাথমিক অর্থনৈতিক জ্ঞানটুকুও নেই। এর অর্থ যাদের ওপর কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের সেই বিষয়ে সামান্য জ্ঞানটুকুরও অভাব; সুতরাং সেই বিশেষ বিষয়টার সমাধানে তাদের কাছ থেকে কি আশা করা যেতে পারে।
অন্য সমস্যাগুলোর ব্যাপারেও এ একই সমস্যা। সদাসর্বদা একদল অজ্ঞ এবং অযোগ্য লোক সমস্যার সমাধানে ব্রতী। সমস্যাগুলো যদিও জীবনের বিভিন্ন কোণ থেকে উদ্ভূত, কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলোর সদস্যবৃন্দ তো একই মান মর্যাদায় তৈরি। ন্যায় বিচার তখনই সম্ভব যদি এসব সদস্যবৃন্দের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য যে জ্ঞান দরকার তা থাকত। এটা অকল্পনীয় যে যারা যাতায়াত ব্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ তারাই আবার বৈদেশিক নীতি নির্ধারণেও দক্ষ; অবশ্য যদি না এরা প্রতিভাসম্পন্ন হয়। কিন্তু পুরো একটি শতাব্দিতে একজনের বেশি প্রতিভা খুব কমই জন্মগ্রহণ করে। তাই এসব ক্ষেত্রে সত্যিকারের প্রতিভাসমৃদ্ধ মানুষের দেখা খুব কমই পাওয়া যায়। বেশির ভাগই সেসব ললিতকলার অনুরাগীবৃন্দ যাদের মন অত্যন্ত সংকীর্ণ এবং একগুয়ে। এরা জঘন্য বেশ্যাবৃত্তিতে পারদর্শী। আর এ কারণেই এসব তথাকথিত সম্মানিত দ্রলোক মহোদয়গণ কোন বিষয়ের ওপর আলোচনা চলাকালে এবং বিচারের সময় এত চপলতা দেখিয়ে থাকে; যেসব বিষয়বস্তু বিচারের সময় বুদ্ধিমান লোকদেরও অতি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। একটা দেশের ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের জন্য যে ধরনের গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশের প্রয়োজন, তা ত এসব সংসদে নেই-ই বরং যে আবহাওয়ায় এসব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়, তা তাসের আড্ডায় ঠিক মানানসই। জনসাধারণের ভাগ্য ঠিক করার চেয়ে তাসের আড্ডায় এসব দ্রমহোদয়দের উপযুক্ত স্থান।
অবশ্য এটা বলা ঠিক হবে না যে এর মধ্যে কোন সদস্যেরই সামান্যতম কর্তব্যজ্ঞানটুকুও নেই। তা অবশ্য প্রশ্নাতীত।
কিন্তু বিশেষ করে এ পদ্ধতিতে যা কিনা একজন ব্যক্তিকে যে বিষয়ে সে দক্ষ নয়, তার ওপর জোর করে তার বিচার আদায় করে নেয়, এর অর্থ হল নৈতিক দিক থেকে তাকে টেনে নিচে নামানো। কেউ-ই সাহস করে বলবে না যে, ভদ্রমহোদয়গণ, আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করছি সে বিষয়ের কিছুই আমাদের জানা নেই। আমি বা আমাদের এ বিষয়টার ওপর কিছুমাত্র যোগ্যতা নেই। অবশ্য এ ধরনের স্বীকারোক্তিতেও খুব বেশি একটা যায় আসে না, কারণ এ ধরনের সোজাসুজি সরলতা বুঝবেই বা কে? যে লোকটি এরকম স্বীকারোক্তি করবে, তাকে সম্ভবত সম্মানিত গাধা হিসেবে ধরে নিয়ে এ রকম মজাদার খেলা নষ্ট করতে দেওয়া হবে না। যাদের মনুষ্যচরিত সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধ্যান ধারণা আছে, তারা ভালভাবেই জানে যে সহকর্মীদের গণ্ডীর মধ্যে কেউ বোকা সাজতে চায় না। এবং এক্ষেত্রে বিশেষ সাধুতাকে বোকামী বলে গণ্য করা হয়।
এভাবে একজন সোজা কথার লোক যখন সংসদে সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়, শেষমেষ হয়ত বা পরিবেশের চাপে পড়ে বিনা আপত্তিতে তাকেও ব্যাপারগুলো মেনে নিতে হচ্ছে, জনসাধারণ তার ওপর যে বিশ্বাস করে সংসদে তাকে পাঠিয়েছিল তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই বলা চলে। তখন ব্যাপারটা হল কোন একজন একক ব্যক্তিত্ব যদি কোন বিশেষ আলোচনায় অংশগ্রহণ না করে, তাতে কিন্তু পরিস্থিতির বিন্দুমাত্র কোন পরিবর্তন হয় না। কিন্তু তার সম্মানটাই মাঝের থেকে ধুলিসাৎ হয়ে যায়। শেষে হয়ত বা সে সদস্য নিজেকে বোঝাতে সমর্থ হয় যে আর যাহোক দলের মধ্যে সে নিকৃষ্ট নয় এবং এসব বিতর্কে অংশগ্রহণ না করে সবচেয়ে খারাপ কিছু ঘটার হাত থেকে রেহাই পায়।
এর বিরুদ্ধেও যুক্তি স্থাপন করা যায়। বলা যেতে পারে যদিও একক কোন ব্যক্তি বিশেষ কোন প্রশ্নের বিতর্কে নিজেকে জড়ানোর মত জ্ঞান নেই, তবু তার ধ্যান-ধারণা তার দলের উপদেশের ওপর নির্ভরশীল, এবং বলা হয়ে থাকে যে তার দল বিশেষজ্ঞদের একটা দল গড়ে, যাদের বিষয়টির ওপর যথেষ্ট জ্ঞান আছে, পুরো ব্যাপারটাই তাদের সামনে রাখা হয়।
হঠাৎ এক নজরে মনে হবে যুক্তিটা যথেষ্ট জোরাল। তবু আরেকটা প্রশ্ন থেকে যায়, যদি বিশেষ কোন সমস্যা সমাধানের জন্য মাত্র কয়েকজনের জ্ঞান থাকে, তবে আর পাঁচশ লোককে নির্বাচন করা কেন?
আসলে আমাদের আধুনিক গণতান্ত্রিক সংসদীয় পদ্ধতির লক্ষ্যই হল বুদ্ধিমান এবং জ্ঞান বিশিষ্ট সদস্যদের একত্রিত না করা। না; একেবারেই নয়। বরং পদ্ধতিটার উদ্দেশ্যই হল একদল অবিবেচক, যাদের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণভাবেই অন্যের ওপরে নির্ভরশীল, যাতে সহজেই তাদের পরিচালন করা যায়। কারণ প্রতিটি একক ব্যক্তিত্ব সংকীর্ণমনা। এ একটা উপায়েই দলীয় আদর্শ আজকের দিনের দুষ্ট স্বরূপ যা প্রকটিত তাকেই কাজে লাগানো যায়। এ পদ্ধতিতেই একমাত্র সম্ভব অদৃশ্য হাতে সবকিছুকে পরিচালনা করা, যাতে নিজেকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখা যায়; আর এ কারণেই তাকে তার কাজের আর হিসেব নিকেশের জন্য তলব করা সম্ভব নয়। এ অবস্থাতে যদি কেউ জাতির পক্ষে বিপর্যয়সূচক কোন পথ ঠিক করে; তবু তার জন্য তাকে দায়ী করা উচিত হবে না। যদিও সবাই জানে তার একক শয়তানি প্রতিভা এর জন্য দায়ী। কারণ পুরো দায়িত্বটা তো গিয়ে পড়ে দলের ঘাড়ে।
বাস্তবে কিন্তু পুরো ব্যাপারটাতেই কার কোন দায়িত্ব থাকে না। কারণ দায়িত্ব যে একক ব্যক্তিত্বের ওপর বর্তানো সম্ভব— সংসদীয় সদস্যবৃন্দের শূন্যগর্ভ চিল্কারে তার প্রতিফলন কি করে হবে?
সংসদ নামক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান পেঁচা ধরনের লোকদেরই আকৃষ্ট করে থাকে, যারা দিনের আলো সহ্য করতে অপারগ। সাহসী এবং সোজা কোন ব্যক্তি, যে তার নিজের কাজের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত,–কখনই এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট হবে না।
এ কারণেই এ তথাকথিত ছাপমারা গণতন্ত্র সে জাতির হাতের যন্ত্রে পরিণত, এরা তাদের নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দিনের আলোর দিকে পেছন ফিরিয়ে থাকে। যা এরা বরাবর করে এসেছে এবং আজও করছে। একমাত্র ইহুদীরাই এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা করে, কারণ এ প্রতিষ্ঠান ওদের মতই দুনীস্তি এবং প্রতারণায় পরিপূর্ণ।
এ ধরনের গণতন্ত্রের ঠিক উল্টোপিঠ হল জার্মান গণতন্ত্র, যাকে সত্যিকারের গণতন্ত্র বলে আখ্যা দেওয়া যায়। কারণ এখানে নেতা নির্বাচন অবাধে হয়ে থাকে এবং তারা তাদের কাজের ত্রুটির জন্য সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিতে সদাসর্বদা প্রস্তুত থাকে। সমস্যাগুলোকে গরিষ্ঠতার ভোটে দেখা হয় না। একক ব্যক্তির দায়িত্ব সেখানে সমাধানের পথ খোঁজে। এবং তার জন্য সে পৃথিবীতে তার যা কিছু আছে সবকিছু বন্ধক দিতে তৈরি এমন কি নিজের প্রাণ পর্যন্ত।
এমন মানুষ পাওয়া সম্ভব কিনা যে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ করবে; এখানে হয়ত বা আপত্তি উঠবে। আপত্তি উঠলে তার উত্তর হল; ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে আমাদের জার্মান গণতন্ত্রের অন্তনিহিত শক্তিই তাকে পদলোভী হয়ে উঠতে দেবে না। যে হয়ত বা বুদ্ধির দিক থেকে নিকৃষ্টতম এবং নৈতিক দিক থেকে অসাধু চালাকির পথ বেয়েই এমন এক জায়গায় উঠেছে যেখান থেকে সে তার সহ নাগরিকদের ওপর শাসনকার্য চালিয়ে যাচ্ছে। জার্মান গণতন্ত্রের এ সুদূরপ্রসারী দায়িত্বের ভয়টাই তাকে অজ্ঞতা এবং শঠতা থেকে দূরে রাখবে।
যদি এর মধ্যে কেউ বুকে হেঁটে অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে তার লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগিয়ে চলে, তবে তাকে চিনে ফেলা কষ্টকর হয় না; এবং কর্কশ কণ্ঠে সে শুনতে পারে; দূরে হঠো বদমাস। এ মাটিতে তোমার পাপ রাখার জায়গা নেই, কারণ এ হাঁটা তাকে সোজা সর্পদেবতার মন্দিরের দ্বারে নিয়ে যাবে, এবং সেখানে নিকৃষ্ট প্রকৃতির কোন লোকের প্রবেশ নিষেধ; একমাত্র মহান চরিত্রের লোকই সেখানে যেতে পারে।
ভিয়েনায় সংসদ সভা দু’বছর পর্যবেক্ষণের পর আমার এ ধারণাই হয়েছিল। এরপর অবশ্য আমি সেখানে আর যাইনি।
এ সংসদীয় গণতন্ত্রই হল অন্যতম কারণ যার জন্য হাবুসবুর্গ সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব শেষের দিকে ক্রমান্বয়ে বারবার ঢলে পড়েছিল। যত বেশি জার্মান প্রভাব ফেঁচে বাদ দেওয়া হচ্ছিল,—ঠিক তত বেশি বিভিন্ন জাতির মধ্যকার ঝগড়াটা প্রকট হয়ে উঠেছিল। রাজকীয় সংসদ পদ্ধতির জন্য সর্বদা জার্মানরা মার খেয়েছে। যার অর্থ হয়েছে সম্রাট সামগ্রিকভাবে নিজের ক্ষতিই ডেকে এনেছে। শতাব্দীর শেষের দিকে সবচেয়ে সোজা এবং নির্বোধ লোকটাও দ্বৈত রাজতন্ত্রের সংযোগশীল শক্তির দ্বন্দ্ব দেখতে পেত, যেটাকে আর কোনরকমই ঢেকে রাখা সম্ভব ছিল না, এবং যা বিভিন্ন জাতিকে আলাদা করার অভিপ্রায়ে নিয়ত টানাটানি করে চলত।
উপরন্তু, প্রদেশগুলো সেদিন স্বনির্ভরতার জন্য যে পথ বেছে নিয়েছিল তা অত্যন্ত সংকীর্ণমনা এবং পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত অসম্মানজনক। শুধু হাঙ্গেরী নয়, সমস্ত প্রদেশগুলোই যারা এ রাজতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তারা এ রাজতন্ত্রের দুর্বলতা বুঝতে পারেনি, আর এ দুর্বলতা যে তাদের পক্ষে কত ক্ষতিকর তা আর কে বোঝাবে। বরং বার্ধক্যজনিত কারণে এ ক্ষয়ে যাওয়াকে অভ্যর্থনাও করেছিল। তারা অপেক্ষা করছিল সুস্থ হওয়ার জন্য নয়; বরং সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়ার দিনটা গুণছিল।
জার্মানসহ নির্যাতিতদের গণতান্ত্রিক সংসদকে ভেঙে ফেলার জন্য সবরকম দাবিই ক্রমেই বেড়ে উঠতে থাকে। সমস্ত দেশ জুড়ে এক জাতের সঙ্গে অপর জাতের সংঘর্ষ চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু মোটামুটি এ সংঘর্ষগুলো প্রায় সবটাই একমুখী; অর্থাৎ জার্মানদের বিরুদ্ধে। বিশেষ করে যখন থেকে সিংহাসনের দাবি বর্তায় আর্চ হিউক ফ্রানজ ফারনান্দের ওপর, চেকেরা সেই সুবিধা নিয়ে শাসনব্যবস্থার উঁচু স্তর থেকে নিচু স্তর পর্যন্ত নিজেদের প্রভাব এবং প্রতিপত্তি বিস্তার করে ফেলে। দ্বৈত রাজকীয়তন্ত্রের উত্তরাধিকারী সমস্ত কিছু সুযোগ সুবিধা নিয়ে জার্মানদের প্রভাব প্রতিপত্তি খর্ব করতে মাঠে নেমে পড়ে, সোজাসুজি না হলেও সে এ পদ্ধতির রক্ষাকর্তা হিসেবে কাজ চালিয়ে যায়। শাসনব্যবস্থার অফিসারদের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে জার্মান জেলাগুলোকে; ধীরে ধীরে চূড়ান্তভাবে মিশ্রভাষার বিপজ্জনক সীমার মধ্যে টেনে আনা হয়। এমন কি অস্ট্রিয়ার নিচের দিকের প্রদেশগুলোতেও একই ব্যবস্থা বলবৎ করা হয়; আর ভিয়েনাকে তো চেকেরা তাদের সবচেয়ে বড় শহর হিসেবে দেখত।
এ নতুন হাবুসবুর্গ রাজপ্রাসাদের লোকেরা নিজেদের মধ্যেই কথাবার্তা চালানোর জন্য চেক ভাষাটাকেই বেশি পছন্দ করত। আর্চ ডিউকের স্ত্রী চেকদেশের রাজকন্যা এবং রাজকুমারের সঙ্গে এ বিয়ে ঠিক সমানে সমানে হয়নি। রাজকুমার সম্বন্ধে বলা যায় তার চেয়ে সব বিষয়ে নিচু এ রাজকন্যাকে বিয়ে করেছিল। রাজকন্যা যে পরিবার এবং পরিবেশ থেকে এসেছিল, সেখানে জার্মানদের বিরুদ্ধাচারণ ছিল বংশপরম্পরায়, রক্তে রক্তে, শিরা উপশিরায়। আর্চ ডিউকের মনের ইচ্ছে ছিল মধ্য ইউরোপে শ্লাভ সাম্রাজ্য বিস্তার করা, যেটা পরিপূর্ণ ক্যাথলিক ধারায় হবে। অর্থাৎ গোঁড়া রাশিয়াকে বাধা দেবার প্রাচীর হিসেবে যাতে এ ক্যাথলিক ধর্ম কাজ করে।
হাবুসবুর্গের ইতিহাসে বারবার এ জিনিসের পুনরাবৃত্তি হয়েছে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ধর্মকে কাজে লাগানো হয়েছে; আর এ ব্যাপারে নিছক শোষণ পদ্ধতিকে কার্যকরী করার জন্য অবশ্যই সেখানে জার্মান স্বার্থ আছে। এর ফলাফল অনেক জায়গাতেই শোকাবহ হয়ে ওঠে।
তবে হাবুসবুর্গ প্রাসাদ বা ক্যাথলিক চার্চ যা আশা করেছিল তা কিন্তু পায়নি। হাবুসবার্গ তার সিংহাসন হারায়, আর চার্চের প্রভাব পুরো দেশটা থেকেই মুছে যায়। ধর্মীয় উদ্দেশ্য রাজনীতিতে ঢালার জন্য আরেকটা উত্তেজনার উদ্ভব হয়।
জার্মান মতবাদকে রাজকুমার রাজতন্ত্রের থেকে উচ্ছেদ করতে গিয়ে জার্মান আন্দোলন সমস্ত অস্ট্রিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে। গত শতাব্দীর আশি সালের দিকে ম্যানচেষ্টার লিবারালিজম যার চিন্তাধারার মূল ভিত্ ছিল ইহুদীরা, এ দ্বৈত রাজতন্ত্রে তার সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে, এর প্রতিক্রিয়াটা ঠিক সামাজিক দিক থেকে আসেনি, এসেছিল জাতীয়তাবাদী থেকে। যেটা পুরনো অস্ট্রিয়ায় সদা সর্বদা হয়ে এসেছে। কিন্তু জার্মানদের নিজেদের অধ্যাবসায় উৎসাহের সঙ্গে প্রাণপণে চেষ্টা করেছে নিজেদের অস্তিত্ব ধরে রাখার। তখন অবশ্য অর্থনৈতিক চাপ মাত্র মাথা চাড়া দিতে শুরু করেছে; কিন্তু তা তো দ্বিতীয় স্তরের সমস্যা। সাধারণ রাজনৈতিক এ বিশৃঙ্খলার থেকে দুটো দলের অভ্যুত্থান হয়। একটা পুরোপুরি জাতীয়তাবাদী, আর অপরটা চরিত্রগত দিক থেকে সামাজিক কিন্তু উভয় দলই ভবিষ্যতের পক্ষে উৎসাহদায়ক এবং উদ্দেশ্যমূলক।
১৮৬৬ সালের যুদ্ধে অস্ট্রিয়ার নির্যাতনের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য হাউস অফ হাবুসবুর্গ তখন বদ্ধপরিকর। শুধুমাত্র সম্রাট ম্যাস্কিমিলিয়ান অফ মেকিকোর করুণ পরিণতিই ফ্রান্সের সঙ্গে খুব নিকট সম্পর্ক স্থাপন করতে দেয় না। ম্যাস্কিমিলিয়ানের সর্বনাশা অভিযানই তৃতীয় নেপোলিয়ানকে ডেকে আনে এবং সত্যি বলতে কি ফরাসী লোকটা তাকে যেভাবে টলটলায়মান অবস্থায় একা ফেলে রেখে সরে পড়ে, তাতে সবারই ঘৃণা মিশ্রিত ক্রোধ জেগে ওঠে। তবুও হাবুসবুর্গ সুযোগের অপেক্ষায় প্রতীক্ষা করেছিল। যদি ১৮৭০-৭১ সালের সাফল্য না আসত, হয়ত বা ভিয়েনায় সাদাওয়া যুদ্ধের প্রতিহিংসার দরুন রক্তগঙ্গা বয়ে যেত।
এ দু’বছরের অর্থাৎ ১৮৭০-৭১ সালের বীরত্বময় সংঘর্ষ আরো একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপারের সৃষ্টি করে; যার জন্য হাবুসবুর্গ বাধ্য হয় তার হৃদয় পরিবর্তনের। অবশ্য সে পরিবর্তন হৃদয়ের অন্তঃস্থলের প্রেরণায় নয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে পড়ে। পূর্বের জার্মানরা গৌরবময় জয়ের পথ দিয়ে জার্মান সাম্রাজ্যে প্রবেশ করে এবং তাদের পূর্বপুরুষদের স্বপ্নের মহৎ পুনরুত্থান প্রত্যক্ষ করে।
এর জন্য অবশ্য এ ব্যাপারে আমাদের কোন ভুল বোঝাবুঝি থাকা উচিত নয়, সত্যিকারের অস্ট্রিয়ার জার্মানরা উপলব্ধি করে যে এ সময় থেকে রাজ্যাভিষেক প্রয়োজন হলেও করুণ পরিণতির জন্য দায়ী, যদিও এটা সাম্রাজ্য পুনস্থাপনের জন্য একটা কর্তব্যও বটে। কিন্তু তা পক্ষাঘাতগ্রস্ত পুরনো কুটুম্বিতার মত শেষমেষ বোঝা হয়ে রুগ্ন ক্ষয়ে যাওয়া রুগীর মত অবস্থায় এসে না দাঁড়ায়। সর্বোপরি, জার্মান-অস্ট্রিয়ান উভয়েই উপলব্ধি করে যে হাবুসবুর্গ প্রাসাদের ঐতিহাসিক দিন শেষ হয়ে এসেছে এবং নতুন সাম্রাজ্যে যে নয়া সম্রাটকে অভিষেক করা হবে, তাকে নায়কোচিত ছাঁচে গড়া হবে, যাতে রাইনের মুকুট পরার যোগ্যতা তার থাকে। এ অভিপ্রায় এবং স্থিরতাই সেই হাবুসবুর্গ প্রাসাদের একটা শাখা বেছে নিতে সাহায্য করে, যে শাখায় ফ্রেডারিক দ্য গ্রেট অতীত দিনে সমগ্র জাতিকে গৌরবের শিখায় তুলে ধরে জাতির মুখ গৌরববাজ্জ্বল করেছিল।
১৮৭০-৭১ সালের যুদ্ধের পর হাবুসবুর্গ প্রাসাদ স্থির মাথায় সমস্ত জার্মানদের নির্মূল করার কাজে নেমে পড়ে, যাদের সম্পর্কে ওদের ধারণা ধীরে ধীরে হলেও একেবারে বিনাশ করা চাই। আমি ইচ্ছে করে নির্মূল’ শব্দটা ব্যবহার করেছি; কারণ এ শব্দটা দিয়েই একমাত্র বোঝানো সম্ভব শ্লাভদের পদ্ধতির ফলাফল কি হতে পারে। যাদের ওপর নির্মূলের বিজ্ঞপ্তি ঝুলছে, তারাই বিদ্রোহের অগ্নিশিখা জ্বালিয়ে তোলে। এবং সেই আগুনের শিখা এতই লেলিহান যে আধুনিক জার্মান ইতিহাস তা কোনদিন প্রত্যক্ষ করেনি।
এ প্রথম জাতীয়তাবাদী এবং দেশপ্রেমিকরা একত্রে বিদ্রোহীতে পরিণত হয়। জাতি বা দেশের বিরুদ্ধে এ বিদ্রোহ নয়। এ বিদ্রোহ হল সরকারের বিরুদ্ধে, যে সরকার তাদের মতে সুনিশ্চিতভাবে জাতিকে ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে, আধুনিক ইতিহাসে এ প্রথম যখন বংশ পরম্পরায় রাজবংশীয় দেশপ্রেমিক এবং জাতীয়তাবাদী দলের পিতৃভূমির প্রতি ভালবাসা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে খোলাখুলি সংঘর্ষ লাগে।
অস্ট্রিয়াতে সর্বব্যাপী জার্মান আন্দোলন, যা গত শতাব্দীর শেষের দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল যে একটা দেশ তার শাসকবর্গের কাছে পরিষ্কার এবং সুষ্টভাবে দাবি জানাতে পারে, তার শাসনকার্য দেশের স্বার্থে পরিচালিত হবে, অথবা কমপক্ষে তা জাতির ক্ষয় ডেকে আনবে না।
শাসকবর্গের শাসন কখনও নিজে থেকে সরে যাবে না। তা হলে তো যে কোন রকম অত্যাচার লঙ্খনীয় এবং পবিত্র বলে বিবেচিত হত।
শাসক যদি তার শক্তি জাতির ধ্বংসের কাছে নিয়োজিত করে, তবে বিদ্রোহ শুধু সঠিক পন্থাই নয়, প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্যও বটে।
এখন প্রশ্ন হল কখন এবং কী ভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হবে, তা শুধু নীরস প্রবন্ধ লিখে সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন শক্তির। হ্যাঁ, শুধুমাত্র শক্তিই এ সমস্যার সমাধান করতে পারে।
প্রত্যেকটি শাসকবর্গ, যদিও এরা নিকৃষ্টতম এবং হাজার বার জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তবু তারা দাবি করবে যে তারা জাতিকে টেনে ওপরে তুলেছে। এর প্রতিপক্ষরা, যারা জাতীয়তাবাদী সংরক্ষণের জন্য সংগ্রাম করে চলেছে তাদেরও উচিত একই হাতিয়ার ব্যবহার করা, যা শাসকবর্গ ব্যবহার করে চলেছে। একমাত্র এ পথেই এ ধরনের অপশাসন রোখা যায় এবং নিজেদের মুক্তি ও স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে পারা সম্ভব। সুতরাং এ সংঘর্ষ আইনগতভাবেই চলবে যতক্ষণ পর্যন্ত শাসক সেই পথে চলবে; কিন্তু বিদ্রোহীর দল বে-আইনী কার্যকলাপও শুরু করতে পারে যদি অত্যাচারী শাসকবর্গ সে পথে চলে।
বিশেষ করে বলতে গেলে, আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে মানবজাতির অস্তিত্বরক্ষা শুধু শাসনকার্যের মধ্যে ব্যাপ্ত থাকে না; অধিকন্তু জাতিকে সংরক্ষিত রাখাই তার প্রধানতম কর্তব্য।
যদি জাতিই বিপন্ন হয়ে পড়ে অথবা নিমূল হওয়ার পথে পা বাড়ায়, তবে আইন টাইন দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রশ্ন। শাসকবর্গ অবশ্য এক্ষেত্রে শুধু আইন অনুযায়ী ব্যবস্থাই নেবে। কিন্তু অত্যাচারিতভাবে নিজেদের রক্ষা করার প্রবৃত্তি সহজাত, সুতরাং যে কোন উপায়ে তা করা উচিত।
একমাত্র এ পথই স্বীকৃত, এ সংগ্রামের নজীর ইতিহাস খুঁজলে ভুরি ভুরি পাওয়া যাবে। নিজেদের অত্যাচারিত শাসকের হাত থেকে বা বিদেশী বন্ধন খুলতে এর কোন বিকল্প নেই।
মানুষের অধিকার শাসকের অধিকারের থেকে অনেক ওপরে। কিন্তু কেউ যদি মনুষ্যত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে পরাজয় স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়, তার অর্থ বিশেষ লক্ষ্যে পৌঁছবার পক্ষে তার প্রয়াস যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।
অস্ট্রিয়া হল একটা পরিষ্কার এবং উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কত সহজে একটা বিক্ষুব্ধতা পোশাকের নিচে আইনের নামে তার মাথা লুকাতে পারে।
হাবুসবুর্গ সাম্রাজ্যের আইনগত শক্তির দিকটার ভিতই ছিল সংসদের জার্মান বিরোধিতা। কারণ সংসদে তখন অজার্মানদের গরিষ্ঠতা, এবং রাজবংশীয়রা যারা বরাবর জার্মানদের বিরোধীতা করে এসেছে। দেশের শাসন ব্যবস্থাটাই এ দুটো বিষয়ের মধ্যে সংঘবদ্ধ। জার্মানদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য এ দুই নিরর্থক বিষয়ের উৎখাতের চেষ্টা করাটাও ছিল নিষ্ফলা। যারা উপদেশ দিত এ আইনানুগ পথে যেতে এবং শাসনব্যবস্থার অনুগত হওয়ার জন্য, তাদের পক্ষে কোন রকম বিরোধিতা করাই সম্ভব নয়। কারণ আইন অনুযায়ী বিরোধিতা করার কোন পথই খোলা নেই। এ আইন বিশেষজ্ঞ সংসদ সদস্যদের উপদেশ মেনে চলার অর্থই হচ্ছে রাজতন্ত্রের মধ্যে জার্মানদের অনিবার্য ধ্বংস; এবং এ ধ্বংস আসতেও বেশি সময় লাগে না। সত্যি বলতে কি সাম্রাজ্য নিজে থেকে ভেঙে পড়ার জন্যই জার্মানরা রক্ষা পায়।
চশমাধারী তাত্ত্বিকরা তাদের নিজেদের মতবাদের জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারে, কিন্তু লোকের জন্য নয়। কারণ মানুষই আইন তৈরি করেছে এবং ক্রমে ক্রমে সে ভাবতে শেখে যে আইনের জন্যেই সে বেঁচে আছে।
জার্মানদের সর্বব্যাপী আন্দোলন এসব নিরর্থক ধারণাগুলো মুছে দিতে সাহায্য করেছিল, যদিও মতবাদধারী তাত্ত্বিক এবং অন্যান্য ভক্তিতে গদগদ পুজারীরা যে এতে চমকে উঠেছিল তাতে সন্দেহ নেই।
যখন হাবুসবুর্গ তাদের হাতের সমস্ত কলাকৌশল নিয়ে জার্মানদের কাছাকাছি আসতে চেষ্টা করে, তখন এ জার্মানরা নিষ্ঠুর হাতে সেই উজ্জ্বল রাজবংশীদের প্রচণ্ড আঘাত করে। এ দলই প্রথম শাসকবর্গের দুর্নীতির মুখোশ খুলে দেয় এবং হাজার হাজার মানুষের জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হয়। এভাবে প্যান্ জার্মান মুভমেন্ট বা সর্বব্যাপী জার্মান আন্দোলন দেশকে রাজবংশীয়দের শোচনীয় আলিঙ্গন থেকে রক্ষা করে।
পার্টি তার প্রথম আর্বিভাবেই বিরাট এক অনুগামীদের আস্থা লাভ করে। কিন্তু প্রথমদিকের সাফল্য বেশি দিন ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। আমি যখন ভিয়েনাতে আসি তখন প্যান্ জার্মান পার্টিতে গ্রহণ লাগা শুরু হয়ে গেছে। খ্রিষ্টান সোশ্যালিস্ট পার্টি ইতিমধ্যে শাসন ক্ষমতা দখল করে বসে আছে। প্যান জার্মান পাটি তখন কৃচ্ছতার গভীরে প্রায় পুরোপুরি নিমগ্ন।
একদিকে প্যান্ জার্মান আন্দোলনের উত্থান এবং পতন, অপরদিকে খৃষ্টান সোশ্যালিস্ট পার্টির চমৎকার অগ্রগতি আমার অনুধাবন করার জন্য বিস্ময়কর বিষয়বস্তু; আর সেই কারণেই আমার ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের পক্ষে এদের দান অপরিসীম।
আমি যখন ভিয়েনাতে আসি, আমার সহানুভূতি ছিল সম্পূর্ণরূপে প্যান্ জার্মান আন্দোলনের দিকে।
বিশেষ করে তাদের জয়ধ্বনি। জয় হোক হোয়েন জোলারেন, আমাকে বিস্ময়ে অভিভূত করে ফেলত; তাদের মনের জোর দেখে আমার বুক ভরে উঠত। তারা নিজেদের অখণ্ড জার্মানির অংশ বলে ভাবত, যেখান থেকে তারা সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন। তারা সুযোগ পেলেই জনসাধারণকে বুঝিয়ে বলত যা আমার শুধু আত্মবিশ্বাসই বাড়িয়ে দেয়নি, উৎসাহও বর্ধিত করেছে। জার্মান সম্পর্কিত সমস্ত আদর্শকে প্রকাশ্যে ঘোষণা করা এবং কোন বিষয়ে আপোষ নয়; আমার মনে হয় এ পথেই শুধু দেশকে বাঁচানো যায়। আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না যে এত বড় একটা আন্দোলন কি করে তাড়াতাড়ি ভেঙে পড়ল; এবং এটা কিছুতেই বোধগম্য নয় যে এত অল্প সময়ের মধ্যে খ্রিস্টান সোশ্যালিস্ট পাটি কি করে এতখানি অগ্রগতি করল। তারা ইতিমধ্যেই জনপ্রিয়তার উতৃঙ্গ শৃঙ্গে চড়ে বসেছে।
যখন এ দুই আন্দোলনকে আমি তুলনামূলক বিচার করতে বসি, তখন ভাগ্য আমাকে সহায় দেয়, এ হতবুদ্ধির সমস্যাটা বোঝায়। ভাগ্যের এ সহায়তা আমাকে যেন আমার পরিবেশে আরো বেশি সংকুচিত করে দেয়।
আমি এখানে দুটো মানুষ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করা, যাদের এ আন্দোলনের স্রষ্টা এবং নেতা বলে মান্য করা উচিত। একজন হল জর্জ ভন্ শ্ৰোয়েনার, আর অপরজন হল ডক্টর কার্ল লুইগার।
ব্যক্তিত্বের দিক থেকে দুজনেই সাধারণের চেয়ে ওপরে এবং তথাকথিত সংসদ সদস্যদের থেকেই উঁচু ছিল। তারা তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করত নিষ্কলঙ্ক, নির্দোষ এবং চরম সাধুতার মধ্যে, চারিদিক যখন দুর্নীতির বিষবাষ্পে আচ্ছাদিত। ব্যক্তিগতভাবে প্রথমে আমি প্যান্-জার্মান প্রতিনিধি শ্রোয়েনারকে পছন্দ করতাম, কিন্তু ধীরে ধীরে খ্রিষ্টান সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতাকে একইভাবে পছন্দ করে ফেললাম।
উভয়ের যোগ্যতা বিবেচনায় আমার মনে হয় গোড়ার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে শ্ৰোয়েনারের চিন্তাধারা উঁচু ধরনের এবং বলিষ্ঠ; সে তার দূরদৃষ্টিতে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের পতন যে কারোর চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্টভাবে দেখতে পেয়েছিল। যদি হাবুসবুর্গ সাম্রাজ্য সম্পর্কে তার কথাগুলোয় জার্মানরা সময় মত মনোযোগ দিত, তবে সর্বনাশা যুদ্ধে সারা ইউরোপের বিরুদ্ধে হয়ত বা জার্মানিকে জড়িয়ে পড়তে হত না।
কিন্তু যদিও শ্রোয়েনার সমস্যার গভীরে ঢোকার ক্ষমতা রাখত, তবে মানুষ চেনার ব্যাপারে তার প্রায়ই ভুল হত।
এবং এখানেই ডক্টর লুইগারের বিশেষ প্রতিভা ছিল। মানুষের চরিত্র বোর ব্যাপারে তার ছিল ইশ্বরদত্ত ক্ষমতা। সে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে মানুষের মূল্যায়ন করত এবং সেই মূল্যায়ন করতে গিয়ে তার প্রাপ্যের চেয়ে বেশি কখনই দিত না। সব পরিকল্পনাই মানুষের বাস্তব দিকটার দিকে নজর রেখে হত, কিন্তু এ বিষয়ের প্রভেদটা শ্ৰোয়েনার ঠিক বুঝত না। প্যান্ জার্মান আন্দোলনের ধ্যান-ধারণাগুলো ঠিকই ছিল, সেগুলো জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে সার্থক করে তুলতে যে দূরদৃষ্টি এবং মনের দৃঢ়তা দরকার তা তার ছিল না। এবং এসব পরিকল্পনা যাতে সহজেই জনসাধারণ দিতে পারে, সেভাবে তৈরি করার ক্ষমতাও তার ছিল না। কারণ জনসাধারণ সম্পর্কে বোধশক্তি ছিল খুবই সীমাবদ্ধ এবং কোনদিনই তার আর বাড়েনি। সুতরাং শ্রোয়েনারের জ্ঞানবুদ্ধি ছিল পয়গম্বরের মত, যা তার পক্ষে কোনদিনই বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।
মানব চরিত্র সম্পর্কে তার বোধশক্তির অভাব, জনসাধারণের শক্তি সম্পর্কেও তাকে ভুল ধারণা দিয়েছিল। শুধু কয়েকটা আন্দোলনের ব্যাপারেই নয় পুরনো প্রতিষ্ঠানগুলোর সহজাত ক্ষমতা সম্পর্কেও।
বাস্তবিকপক্ষে শ্ৰোয়েনার বুঝতে পেরেছিল যে সব সমস্যার তাকে মুখোমুখি হতে হচ্ছে, সেগুলো সব মানবিক। কিন্তু তার পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না যে একমাত্র জনসাধারণই সেই সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারে, কারণ সেগুলো ছিল ধর্মঘেষা।
দুর্ভাগ্যবশত তথাকথিত বুর্জুয়াদের সংগ্রাম শক্তি সম্পর্কেও তার ধারণা ঠিক ছিল। এ দুর্বলতা মূলত তাদের নিজেদের ব্যবসার স্বার্থরক্ষার কারণে এবং তারা যে বিষয়ে এককভাবে কোনমতেই কোনরকম দায়িত্ব বা ঝুঁকি নিতে রাজী ছিল না। এটাই তাদের যে কোন সংগ্রামে অংশ নিতে বাধা দিয়েছে। বিশেষভাবে বলতে গেলে সর্বাত্মক আন্দোলন কখনই সার্থকতা লাভ করতে পারে না, যদি না বিশাল জনসাধারণ তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে তাতে অংশগ্রহণ না করে।
জনসাধারণের এ নিচেকার স্তর সম্পর্কে ভুল ধারণা সামাজিক সমস্যাগুলো সম্পর্কেও সঠিক ধারণা থেকে তাকে বঞ্চিত রাখে।
এসব ব্যাপারে ডক্টর লুইগার ঠিক শোয়েনারের বিপরীতপন্থী ছিল। মানব চরিত্র সম্পর্কে তার সাধারণ জ্ঞান বিভিন্ন সামাজিক শক্তিগুলো সম্বন্ধে তার ধারণাকে সঠিকভাবে উপস্থাপিত করে এবং বর্তমান প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে অবহেলার মনোভাব নেওয়ার হাত থেকে তাকে রক্ষা করে; এবং সম্ভবত তার এ গুণটাকেই সে ব্যবহার করে এসব প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কাজে লাগায়।
আমাদের সেই ঘটনাবহুল কালে, সে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল যে সমাজের ওপরের স্তরের সংগ্রাম করার ক্ষমতা বলতে কিছু নেই, এবং নতুন নতুন বড় সংগ্রাম করতেও তারা অসমর্থ, যতক্ষণ না পর্যন্ত বোঝে যে এ আন্দোলনে জয় তাদের সুনিশ্চিত। সুতরাং সমাজের এ বিশেষ স্তরটাকে জয় করার জন্য সে প্রাণমন ঢেলে দেয় এবং তাদের পঙ্গু করার চেয়ে সযত্নে সাময়িক উদ্দীপনা তাদের মধ্যে লালন পালন করে; কারণ এদের অস্তিত্বই তখন বিপন্ন। দীর্ঘস্থায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর সমর্থন পাওয়ার জন্য সত্বর যত রকমের উপায় বেছে নেওয়া সম্ভব; তার সবগুলোকেই সে গ্রহণ করেছিল; যাতে তার এ আন্দোলনের জন্য সেইসব প্রাচীন প্রতিষ্ঠানগুলোর থেকে যতটা সম্ভব শক্তি আরোহণ করা যায়।
এ কারণে সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে, যাদের প্রায় নির্মূল করার জন্য সরকার উঠে পড়ে লেগেছিল, দলের ভিত্ হিসেবে তাদের নির্বাচন করে। এভাবে সে যে অনুগামীরা দল তৈরি করে, যারা নিজেদের উৎসর্গ করতেই যে সব সময় প্রস্তুত ছিল শুধু তাই নয়, তাদের মধ্যে সংগ্রাম করার মত যথেষ্ট মানসিক শক্তিও বর্তমান। ক্যাথলিক চার্চের প্রতি তার ধ্যান ধারণা যুবক পাদ্রীদেরও দলে টানে এবং প্রাচীন পুরুতের দল একরকম বাধ্য হয়েই রক্ষণক্ষেত্র থেকে রণে ভঙ্গ দেয়; যুবকরা এ আশাতেই নতুন দলে যোগ দিয়েছিল যে ধীরে ধীরে নতুন পার্টি তাদের ওপরে উঠতে সাহায্য করবে।
একমাত্র তার চরিত্রের এদিকটাকে বিচার করার অর্থই হল তার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা। কারণ তার যুদ্ধ কৌশল ছিল অনন্য। সংস্কারক হিসেবে তার প্রতিভাকেও কোনমতেই ছোট করে দেখা চলে না। কিন্তু এসব ক্ষমতা অর্থাৎ অস্তিত্ববোধ এবং যোগ্যতা ছিল সীমাবদ্ধ।
এ বিখ্যাত ব্যক্তিটির লক্ষ্য ছিল কিন্তু সত্যিকারের বাস্তব সম্মত। তার ইচ্ছে ছিল ভিয়েনা জয়ের, যা হল রাজতন্ত্রের হৃদয়স্বরূপ। এ ভিয়েনা থেকেই অসুস্থতা এবং বার্ধক্যহেতু জরাজীর্ণ সাম্রাজ্যের শেষ নাড়ীর স্পন্দন শোনা যেত। যদি কোনভাবে হৃদয়টাকে সুস্থ করে তোলা যায়, তবে শরীরের অন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোও সজীব হতে বাধ্য।
ধারণাটা আদর্শগতভাবে ঠিকই ছিল; কিন্তু যে সময়ের মধ্যে এ আদর্শকে রূপায়িত করতে হবে তা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এবং এটাই হল তার দুর্বল স্থান।
শহর ভিয়েনার মেয়র হিসেবে তার কার্যাবলী অসাধারণ; কিন্তু তাতেও রাজতন্ত্র রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। কারণ পুরো ব্যাপারটাই তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।
তার প্রতিদ্বন্দ্বী শ্ৰোয়েনার কিন্তু ব্যাপারগুলোকে স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পেরেছিল। ডক্টর লুইগার যে বিষয়গুলোর বাস্তব প্রয়োগ করেছিল, তা কার্যকরী হয়নি। শ্রোয়েনার শেষ ধাপ বলে যা ভেবেছিল, সেখানে পৌঁছতে পারেনি। কিন্তু তার আশঙ্কাগুলো আশ্চর্যজনকভাবে সত্যে পরিণত হয়েছিল। এভাবে উভয়েই তাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। লুইগার অস্ট্রিয়া রক্ষা করতে পারেনি, আর শ্রোয়েনারের পক্ষে অস্ট্রিয়ার জার্মানদের পতন রোধ করা সম্ভব হয়ে উঠেনি।
এ দুই দলের পতনের কারণ আমাদের যুগের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা বিশেষ।
আমার বন্ধুদের পক্ষে ব্যাপারটা যে বিশেষভাবে উপকারি হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ অনেক বিষয়েই সেদিনের সেই পরিবেশ ও আমাদের সময়ের মিল ছিল। সুতরাং এ শিক্ষা থেকে শেখা উচিত ছিল যে ভুলগুলো আন্দোলনটাকে খতম করে দিয়ে পুরো জমিটাকে বন্ধ্যা করে দিয়েছিল, তা থেকে রেহাই পাওয়ার।
আমার মতে অস্ট্রিয়াতে প্যান-জার্মান আন্দোলনের ধ্বংসের জন্য মূলত তিনটে কারণ দায়ী।
প্রথম কারণ হল, তৎকালীন নেতাদের সামাজিক সমস্যাগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণা ছিল না। বিশেষ করে নতুন আন্দোলন যেটা চরিত্রগতভাবে বিদ্রোহাত্মক।
শ্ৰোয়েনার এবং তার অনুগামীদের দল তাদের মনোযোগ পুরোপুরি বুর্জোয়া শ্রেণীর ওপর দিয়েছিল; সুতরাং তাদের সেই আন্দোলন নিরীহ এবং মধ্যমগোছের আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। ভাল সময়ে অর্থাৎ সুশাসনের সময় সমাজের বিশেষ স্তরের এ মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধীয় ধ্যান ধারণা দেশের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। কিন্তু খারাপ শাসকের সময়ে এ বিশেষ গুণটাই ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অধ্যাবসায় পূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্যা-জার্মান আন্দোলনকারীদের উচিত ছিল জনসাধারণকে জয় করার। এ ব্যর্থতার জন্য আন্দোলনটির প্রাথমিক কোন আবেগের ঢেউ-ই ছিল না, এবং এ কারণেই আন্দোলনটাতে এত অল্প সময়ে ভাটা পড়ে যায়।
অসংখ্য আধুনিক বুর্জয়া যারা এ আন্দোলনে শামিল হয়েছিল, এর অন্তনির্হিত আবর্তন স্থির করে এবং এ উপায়ে আগে থেকেই জনসাধারণের সমর্থন আশা করে। এ পরিবেশে এ ধরনের একটা আন্দোলন বিতর্ক সমালোচনার পরিধি ছাড়িয়ে ওপরে উঠতে পারে না। ধর্মোন্মাদনা এবং আত্মোৎসর্গের প্রেরণা এ আন্দোলনে আর ছিল না। তার পরিবর্তে জায়গা নিয়েছিল দেশের বর্তমান সরকারের সবকিছুকে মেনে নেওয়া এবং কঠিন সমস্যাগুলোকে ঠেলে এককোণে সরিয়ে দিয়ে এক অপমানজনক শক্তির মধ্য দিয়ে সব কিছুর সমাপ্তি ঘোষণা করা।
প্যান-জার্মান আন্দোলনের জন্য দায়ী হল এর নেতারা, যাদের উচিত ছিল সাফল্যের কারণে অনুগামীর দল বিশাল জনসাধারণের মধ্যে থেকে খুঁজে বের করে নেওয়া।
এভাবে পুরো আন্দোলনটাই গিয়ে পড়ে বুর্জুয়া, সমাজের তথাকথিত ব্যক্তিবর্গ এবং আধুনিক পন্থীদের হাতে। এ অসফলতার দরুন দ্বিতীয়বার ধস্ নামে।
প্যান-জার্মান আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে অস্ট্রিয়ার জার্মানদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। অস্ট্রিয়ার জার্মানদের নির্মূল করার জন্য পার্লামেন্টকে যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। শেষ সময়ে এ অস্ট্রিয়ার জার্মানদের রক্ষা করার একমাত্র পথ ছিল এ সংসদ গণতন্ত্রকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। কিন্তু তার আশা খুবই কম বা ছিল না বললেই চলে।
সুতরাং প্যান্-জার্মান আন্দোলনের মূল প্রশ্ন হল এখন কি করা? সংসদীয় গণতন্ত্রের ভেতরে থেকে তাকে সাবোতাজ করা, নাকি বাইরে থেকে প্রচণ্ড আক্রমণ করে প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দেওয়া।
প্যান-জার্মানরা পার্লামেন্টে ঢুকে পরাজিত হয়েই ফিরে আসে। কিন্তু নিজেদের পার্লামেন্টে ঢুকতে পারার জন্য কৃতজ্ঞ বোধ করে।
বাইরে থেকে এ ধরনের সংগ্রাম চালানোর জন্য প্রয়োজন হল অদম্য ও অজেয় সাহসের এবং আত্মোৎসর্গের প্রেরণাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা। এ সব ক্ষেত্রে যাড়কে শিঙ ধরে জোর করে বলপূর্বক অধিকৃত করতে হয়। ক্রুদ্ধশক্তি হয়ত বা আক্রমণকারীকে বারবার মাটিতে আছড়ে ফেলবে, তবু বলিষ্ঠ মনের জোরে তাকে উঠে দাঁড়াতে হবে, যদিও হয়ত বা তার ইতিমধ্যে কিছু হাড় ভেঙে গেছে, এবং এ ধরনের দীর্ঘ যুদ্ধের পরই একমাত্র বিজয়ী হওয়া সম্ভব। নতুন যোদ্ধারা এ আত্মোৎসর্গের প্রেরণাতেই এসে জোটে। এ অদম্য উৎসাহ শেষমেষ তাদের মাথায় বিজয়ীর মুকুট পরিয়ে দেয়।
এ ধরনের ফলাফলের জন্য অবশ্য জনসাধারণের মধ্যে মহৎ সন্তানের প্রয়োজন। তাদেরই একমাত্র প্রয়োজনীয় মানসিক ধৈর্য এবং অধ্যবসায় থাকে যার দ্বারা কোন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সমাপ্তি করা সম্ভব। কিন্তু প্যান জার্মান আন্দোলনে এ ধরনের কোন যোদ্ধা ছিল না; সুতরাং সমাধানের জন্য সংসদে ঢোকা ছাড়া গত্যন্তর কোথায়!
এটা মনে করলে ভুল হবে যে নৈতিক দিক থেকে অন্তর্জগতে দ্বিধাদ্বন্দ্বের পর এ পথ স্থির করা হয়েছিল বা এটা সুচিন্তিত কোন চিন্তাধারার ফসল। না, এ সমস্যা সমাধানের জন্য অন্য কোনরকম চিন্তাই করা হয়নি। তারা মিথ্যা ধারণা আর ভুল চিন্তাধারার বশবর্তী হয়েই আর চিন্তা করেনি যে এ প্রতিষ্ঠানে মাথা গলাবার কি ফলাফল হতে পারে, যদিও বরাবর আদর্শগতভাবে এ প্রতিষ্ঠানে ঢোকার বিরোধিতা নিজেরাই করে এসেছে। আশা করেছিল এ পথেই তারা জনসাধারণের নিকট পৌঁছতে পারবে। কারণ তাদের কথা যারা শুনবে তারাই তো সম্ভাব্য জাতির প্রতিনিধি। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় শয়তানির একেবারে গোড়ায় ঘা দিতে পারবে, বাইরে থেকে যেটা কোনমতেই সম্ভব নয়। তাদের বিশ্বাস ছিল সংসদের মুক্তির মধ্যে তারা যদি নিজেদের রক্ষা করতে পারে, তবে একক ব্যক্তিত্বের ভূমিকাটা হবে কোন নাটকের মত, যা দিনে দিনে দৃঢ় এবং বর্ধিত হবে।
কিন্তু বাস্তবে পুরো ব্যাপারটাই বিপরীতভাবে দেখা দেয়। বিচারালয়, যার সামনে প্যান-জার্মান আন্দোলনের প্রতিনিধিবর্গ তাদের বক্তব্য উপস্থিত করে, তা মোটেই বিশাল হয়ে ওঠে না। বরং ক্ষুদ্রই হয়েছিল। উপস্থিত তারাই থাকত যারা ওদের বক্তব্য শুনতে রাজী; অন্যেরা পরেরদিন সংবাদপত্রে তা পড়ে নিত।
সংসদ কিন্তু প্রধান বিচারালয় নয়, সবচেয়ে বড় বিচারখানা হল জনসাধারণের সামনে খোলা আকাশের নিচে সভা করা। কারণ এখানেই হাজার হাজার লোকের জমায়েত, এবং তারা শুনতে আসে বক্তা কি বলছে; কিন্তু সংসদে শ্রোতা বলতে তো মাত্র কয়েকশ লোক। এবং বেশিরভাগই সেখানে উপস্থিত থাকে তাদের ধার্য দৈনিক ভাতা পাওয়ার ধান্ধায়, জ্ঞানের আলোকবর্তিকার শিখা বাড়াবার জন্যে নয়; এরাই তথাকথিত জনসাধারণের প্রতিনিধি।
তবে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে জমায়েতে জনসাধারণ কিছু শিখতে আসে না, কারণ শেখার জন্য যতটুকু বুদ্ধিমত্তা এবং ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজন, তা তাদের কারোরই প্রায় থাকে না।
এ সংসদের একজন প্রতিনিধিও সত্যের কাছে শ্রদ্ধাবনত হয়ে নিজেকে কাজের জন্য উৎসর্গ করে না। এ ভদ্রসম্প্রদায়ের একজনও এ কাজ করবে না, যদি না ভাবে আগামীবারে নির্বাচনে সে আবার একই জায়গা থেকে সংসদের সদস্যপদ নির্বাচিত হওয়ার আশা রাখে। সুতরাং এসব সদস্যরা তখনই নতুন পার্টির খোঁজে বের হয় যাদের ভোটে জেতার সম্ভাবনা আছে, যখন দেখে তার পুরনো দলের খারাপ সময় চলছে। অবশ্য এ দল পরিবর্তনের আগে যুক্তির বন্যায় নিজেদের নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং যখনই দেখা যায় বর্তমান পার্টি নির্বাচনে পরাজয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে, তখন দলে দলে নেতাদের দল ভেঙে নতুন দলে যেতে দেখা যায়। সংসদীয় ইঁদুরের দলে তখন জাহাজ ছাড়ার হিড়িক পড়ে।
কোন একক ব্যক্তিত্বের বিষয়বস্তুর ওপর দখলের জন্য এগুলো হয় না। এ দল ভাঙাভাঙির খেলা হয় কোন এক অতীন্দ্রিয় বিষয়ে অন্তদৃষ্টির জন্য। সংসদ মাছির দল ঠিক মুহূর্তে অন্য পার্টির বিছানায় পোকার মত লাফিয়ে পড়ে। আর এসব বিচারালয়ের সামনে বক্তৃতা করা হল বিশেষ কোন জন্তুদের দিকে মুক্তা নিক্ষেপ করা। বাস্তবিকপক্ষে এত কষ্টের কোন প্রতিদান পাওয়া যায় না। কারণ ফল তো সর্বদাই নেতিবাচক।
এবং এটাই সব সময় হয়ে এসেছে। প্যান-জার্মান সদস্যরা হয়ত বা কর্কশ কণ্ঠে চিৎকার করে গেছে, কিন্তু তাদের কথা শুনছেটা কে!
সংবাদপত্রগুলো হয় গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না, না হয় কেটে হেঁটে সেই বক্তৃতাগুলো এমনভাবে প্রকাশ করে যে তার মধ্যেকার সার বস্তুই ধ্বংস হয়ে যায়, অথবা সেগুলোকে এমনভাবে মোচড় দেওয়া হয় যে তার অর্থ একেবারে অন্যরকম হয়ে দাঁড়ায়। যা পড়ে সাধারণ দর্শক নতুন আন্দোলন সম্পর্কে ভুল ধারণা নিয়ে বসে থাকে। একক সদস্যরা কি বলছে সেটা অপ্রয়োজনীয়। দরকার হল সেই বক্তৃতা সাধারণ মানুষ কিভাবে পড়ছে এবং নিচ্ছে।
সুতরাং প্রকাশিত সংবাদপত্রে বক্তৃতাগুলো আর কিছুই নয়, প্রদত্ত বক্তৃতার কাট-ছাঁট করা অংশবিশেষ; যা পাঠকগণকে অসংলগ্ন স্বচ্ছতার ধারণা দেয়। কিন্তু এটা করা বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। সুতরাং দর্শক বলতে সত্যি বোঝায় মাত্র পাঁচশ লোক; এবং তাই যথেষ্ট। নিকৃষ্টতম হল নিচের বিষয়বস্তুটা
প্যান্-জার্মান আন্দোলনটা হয়ত বা সফল হত যদি তার নেতারা উপলব্ধি করতে পারত যে আন্দোলনটা যতটা নতুন পার্টির জন্য তার চেয়ে বেশি সর্বমানবাত্মক চরিত্রের। এ একটাই উপলব্ধি এত বড় একটা সগ্রাম চালানোর জন্য যে অন্তনিহিত শক্তির দরকার, তা জাগাবার জন্য যথেষ্ট। অবশ্য এ ধরনের সগ্রাম চালানোর জন্য প্রয়োজন নেতাদের অসীম বুদ্ধিমত্তা এবং অদম্য সাহস। যদি এ সর্বাত্মক আন্দোলন যারা চালনা করবে তারা তাদের সবকিছু উৎসর্গ করতে প্রস্তুত না থাকে, তাহলে শীঘ্রই দেখতে পাবে এমন অনুরাগী আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, যারা এ সংগ্রামের সাফল্যের জন্য নিজেদের জীবন শুদ্ধ তুচ্ছ বলে মনে করে। যে তার নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম করে,–সে সমাজকে সেবা করবে কি করে?
সাফল্যের পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য প্রত্যেকের উচিত এটাকে এমনভাবে পরিচালনা করা যাতে ভাবী বংশধরেরা এটাকে সম্মান এবং গৌরবের চোখে দেখে; তবে এ আন্দোলনের বেশি সংখ্যায় সভ্যদের কোনরকম প্রতিদান আশা করা অন্যায়। যদি এ ধরনের আন্দোলনে বেশি সংখ্যায় সভ্যদের ঊচুপদ এবং চেয়ার পাওয়ার সুযোগ থাকে তবে প্রচুর পরিমাণে অযোগ্য সভ্যরা সেই দলে ভিড় করবে। এবং দিনে দিনে মুনাফাখোরদের দলই পার্টির ভেতরে বেশি গুরুত্ব পাবে। সত্যিকারের যোদ্ধার দল যারা প্রথম দিকে আক্রমণের প্রচণ্ড ধাক্কা সামলাবে তাদেরই হয়ত বা মুনাফাখোরের দল। পরিত্যক্ত পাথরকুচির মত বাতিল করে দেবে। সুতরাং আন্দোলনের মৃত্যু তো সেখানেই ঘটে যাবে।
একবার যখন প্যান-জার্মান আন্দোলনকারীরা ঠিক করে যে সংসদের সঙ্গে হাত মিলাবে, তখন নেতা এবং যোদ্ধারা আর জনপ্রিয় আন্দোলনের অংশগ্রহণকারী থাকে না, সংসদে সদস্যে পরিণত হয় তারা। এভাবে আন্দোলন সাধারণ একটা রাজনৈতিক দলে পরিণত হয় এবং তার যুদ্ধপ্রিয় চরিত্র হারিয়ে ফেলে; কোনক্রমেই আর শহীদ হতে চায় না।
সগ্রামের পরিবর্তে প্যান-জার্মান আন্দোলনের নেতারা বক্তৃতা আর দর কষাকষিতে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে। নতুন সংসদ সদস্যরা এ ভেবে খুশি হয় যে সর্বাত্মক আন্দোলন চালানোর জন্য বাগ্মিতা অনেক ভাল অস্ত্র; এতে নিজেদের জীবনের ঝুঁকি কম, যা তাকে পদে পদে সশস্ত্র আন্দোলনের সময় মুখোমুখি হতে হয় এবং তাতে যে কোন সময়ে তার জীবন হারাতে হতে পারে। এ সগ্রামের ফলাফল কি হবে তা যেমন বলা যায় না তেমনি ব্যক্তিগত লাভও এতে নেই।
তারা যখন সংসদের সভ্যপদ অলংকৃত করে, তখন তাদের অনুগামীর দল কোন এক অত্যাশ্চর্য কিছু ঘটবে ভেবে আশা নিয়ে বাইরে অপেক্ষা করে। স্বভাবতই কোন অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে না, ঘটতেও পারে না। কিন্তু আন্দোলনের অনুগামীর দল শীঘ্রই অধৈর্য হয়ে পড়ে; কারণ তারা সংবাদপত্রে যা পড়ে; তার সঙ্গে নির্বাচনের কোন প্রতিশ্রুতির মিলই ভোটদাতারা খুঁজে পায় না। তার কারণ অবশ্য বেশি খোজার দরকার। নেই। এর প্রধানতম কারণ হল সাংবাদিকরা প্যান-জার্মান আন্দোলনের নেতারা বাস্তবে কি করছে না করছে তার সত্যিকারের বিবরণ কখনই প্রকাশ করে না।
নতুন সংসদ সদস্যদের দল সংসদের ভেতরে বিদ্রোহী মনোভাবের খুব অল্প ছাপই। রাখে।
প্রকাশ্য জনসভা করাও দিনের পর দিন কমে আসে; যদিও এটাই হল জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার এবং তাদের কাছে পৌঁছবার একমাত্র পথ। কারণ এখানে জনসাধারণের ওপর সোজাসুজি প্রভাব ফেলা যায় ও বিরাট জনসমর্থনও পাওয়া যায়।
বিরাট বীয়ার হলের টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে হাজার হাজার শ্রোতার সামনে যে বক্তারা তাদের বক্তৃতা রাখত তারা যখন সেই টেবিল খালি করে সংসদের উচ্চ বক্তৃতামঞ্চে সামান্য কয়েকজন নির্বাচিত সদস্যদের সামনে তাদের বক্তৃতা রাখে, তখন তাদের বক্তৃতা আর জনসাধারণের কাছে উপস্থিত হয় না, হয়ে দাঁড়ায় নির্বাচিত কয়েকজন সদস্যর উদ্দেশ্যে। এবং প্যান-জার্মান আন্দোলন তার নিজস্ব চরিত্র হারিয়ে ফেলে নিছক একটা ক্লাবে পরিণত হয় যেখানে কঠিন সমস্যাগুলোরও কেতাবী ঢঙে আলোচনা চলে।
সংবাদপত্রের মাধ্যমে দলের যে ভুল ধারণা গড়ে ওঠে, ব্যক্তিগত সম্পর্কের দ্বারা সেটাকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টাও করা হয়নি। যেটা একমাত্র প্রকাশ্য জনসভার মাধ্যমেই সম্ভব, যেখানে একক কোন ব্যক্তিত্ব তার কাজের হিসেব নিকেশ দাখিল করার সুযোগ পায়। এর চরম পরিণতি হল প্যান-জার্মান শব্দটাই বিশাল জনসাধারণের কানে বিষবৎ শোনায়।
আজকের কলমের যোদ্ধাগণ এবং সাহিত্যের চালিয়াতের দলের বোঝা উচিত যে পৃথিবীর ইতিমধ্যে পরিবর্তন সংগঠিত হয়েছে, সেটা রাজহাঁসের পাখার কলমে হয়নি। না; কলমের প্রধান কাজ হল এ পরিবর্তনের তাত্ত্বিক দিকটার ব্যাখ্যা করা। বক্তৃতাই একমাত্র যাদুশক্তি যা ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে যাদুদণ্ডের মত কাজ করে।
বিরাট জনসাধারণকে একমাত্র বক্তৃতা দ্বারাই শাসন করা যায়, অন্য কোন শক্তি দিয়ে নয়। সমস্ত জনপ্রিয় আন্দোলনই হল মহান আন্দোলন। মানুষের ইচ্ছা এবং অনুভূতির এগুলো হঠাৎ আগ্নেগিরির উদ্গীরণ নিষ্ঠুর ধ্বংসের কাজে অথবা জাতিগড়ার কাজে নিয়োজিত হয়। কোন ক্ষেত্রেই মহান কোন আন্দোলন ড্রইংরুমের নায়কদের চিনি মিশ্রিত কবিতা এবং রঙিন কল্পনার দ্বারা সংগঠিত হওয়া সম্ভব নয়।
একটা জাতির ধ্বংস একমাত্র প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই এড়ানো সম্ভব। কিন্তু যাদের মধ্যে প্রবল ইচ্ছাশক্তি বর্তমান, তারাই অপরের মধ্যে সেই ইচ্ছাশক্তির ঢেউ জাগাতে পারে। একমাত্র নেতাদের মধ্যেকার ইচ্ছাশক্তির বন্যা হাতুড়ির আঘাতের মত জনসাধারণের হৃদয়ের দুয়ার খুলতে সমর্থ।
যে এ অনুভূতির প্লাবন তাকে বক্তৃতার মাধ্যমে রূপ দিতে সক্ষম নয়, তার পক্ষে দূরদর্শী এবং তার ইচ্ছার আগামীদিনের দূত হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং একজন তাত্ত্বিক লেখক তার কালি দোয়াত নিয়ে প্রশ্নোত্তরেই ব্যস্ত থাকবে। কারণ তার যোগ্যতা এবং জ্ঞান দুইই বর্তমান, কিন্তু সে জননেতা বা নেতা নির্বাচিত হওয়ার জন্য জন্মায়নি।
প্রতিটি আন্দোলন, যার শেষ পর্যায়ে কেন মহান রূপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা সে ধরনের আন্দোলনে সব সময় নজর রাখতে হবে যেন সেটা জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে। প্রত্যেকটা সমস্যাকে এ দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করার প্রয়োজন, এবং সেই সমস্যা সমাধানের জন্য যে পথ বাছা হবে সেখানে আদর্শের সঙ্গে যেন ছন্দও বজায় থাকে।
এ আন্দোলনে এমন সব কিছুকে পরিত্যাগ করা দরকার—যা নাকি সেই আন্দোলনকে জনতার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে। এটা সহজ সরল সত্য যে কোন মহৎ আন্দোলনই জনসাধারণের শক্তিছাড়া সফল হতে পারে না। তা যত সম্ভ্রম বা উন্নতমানেরই আপাতদৃষ্টিতে দেখাক না কেন। একমাত্র নগ্ন, বাস্তব উদ্দেশ্য সাফল্যের দরজায় পৌঁছে দিতে পারে। কঠিন এবং বাস্তব রাস্তা ধরে হাঁটার অনিচ্ছাই হল আমাদের নিজস্ব লক্ষ্যে না পৌঁছানো এবং এ অনিচ্ছা ইচ্ছাকৃতই হোল্ক আর অনিচ্ছাতেই হোক।
যে মুহূর্তে প্যান্-জার্মান আন্দোলনের নেতারা সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে, সেই মুহূর্ত থেকেই তারা জনসাধারণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন; এবং মুহূর্ত কয়েকের সস্তা সাফল্যের জন্য তারা তাদের ভবিষ্যৎকে উৎসর্গ করে বসে থাকে। তারা সংগ্রামের জন্য সহজ পথটা বেছে নেয় এবং তা নিতে গিয়ে বিজয়ীর পক্ষে অযোগ্য বলে নিজেদের প্রমাণ করে।
ভিয়েনা থাকাকালীন আমি গভীরভাবে এ দুটো প্রশ্ন অনুসরণ করেছি। এবং উপলব্ধি করেছি যে প্যান-জার্মান আন্দোলন ধসে পড়ার পেছনের কারণগুলো হল, এ প্রশ্নগুলোই পুরোপুরি বিশ্লেষণ না করা। আমার ধারণা সেই সময়ে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল অস্ট্রিয়ার জার্মানদের দ্বারা।
এ দুই বিরাট ভুলই হল প্যান-জার্মান আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পারস্পরিক প্রধান কারণ। অন্তর্নিহিত শক্তি যা মহান আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রেরণা দেয়, তা আসে জনসাধারণের কাছ থেকে। কিন্তু সেই জনসাধারণের প্রেরণা থেকেই আন্দোলন বঞ্চিত হয়েছিল। এর ফলাফল হল সামাজিক সমস্যাগুলোর সমাধানের কোন চেষ্টা করা হয়নি এবং এ আন্দোলনের মাধ্যমেও সমাজের নিচু এবং দুর্বল শ্রেণীর মন কাড়ার চেষ্টা করেনি। আরেক ফলাফল হল সংসদীয় গণতন্ত্র স্বীকার করে নেওয়া—যার প্রতিক্রিয়া হয় আগেরই মত।
যদি জনসাধারণ আন্দোলনের সময়ে যে শক্তির পরিচয় দিয়েছে তার সঠিক মূল্যায়ন করা হত, সামাজিক সমস্যাগুলোর প্রতি নজর দেওয়া হত এবং প্রচার সম্পর্কে অন্য পদ্ধতি নেওয়া হত, তবে আন্দোলনের ভারকেন্দ্র সংসদে না গিয়ে রাস্তায় এবং কলকারখানায় ছড়িয়ে পড়ত।
তৃতীয় ভুলটা হল জনসাধারণের মূল্যায়নের শিকড়টাকে খুঁজে বার করার কোন চেষ্টাই হয়নি। কোন অসাধারণ প্রতিভাবান লোক দিয়ে বিশেষ একটা নির্দিষ্ট দিকে জনসাধারণের গতিটাকে ঠিক করে দিতে হয়। জনসাধারণ যখন একবার সেই গতিতে চলে তখন যন্ত্র নিয়ামক ভারী চক্রের মত আপন ভরবেগেই সে চলতে থাকে, বাইরের আর কোন শক্তিরই তাকে চালাতে প্রয়োজন হয় না।
প্যান-জার্মান নেতাদের ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নীতিটার মধ্যেই ভুল ছিল, কারণ ক্যাথলিক চার্চ মানুষের আধ্যাত্মিকতার দিকটাতে তেমন গুরুত্ব আরোপ করেনি।
নতুন দল যে রোমের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রচারে নেমে পড়েছিল তার কারণগুলো নিচে বলা হলঃ।
হাউস অফ হাবুসবুর্গ যখন অস্ট্রিয়াকে একটা শ্লাহু প্রদেশে পরিণত করতে চাইল, তখন তারা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে কোন রকম পথ বেছে নিতে কসুর করেনি।
এমন কি এ নতুন প্রদেশ গড়তে গিয়ে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে শুদ্ধ প্রতারিত করতে তাদের বিবেকে এতটুকু বাঁধেনি। অনেকগুলো পদ্ধতির একটা হল চেক্ ধর্মযাজকদের পল্লীগুলো এবং তাদের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে অস্ট্রিয়াকে শ্লাভ নেতৃত্ব দেওয়ার পথ করে দেওয়া। পদ্ধতিটা ছিল এরূপ :
জার্মান জেলাগুলোতে চেক ধর্মযাজকদের পল্লী জোর করে বসিয়ে দেওয়া হয়। তারপর ধীরে ধীরে সেই ধর্ম যাজকদের চার্চের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে দিয়ে তাদের এগিয়ে দেয়, এভাবে জেলাগুলোকে জার্মান ছাড়া করার কাজে শ্লাভ যাজকপল্লী এবং যাজকেরা তৎপর হয়ে ওঠে।
দুর্ভাগ্যবশত অস্ট্রিয়ার জার্মান পাদ্রীরা এ পদ্ধতির বিরোধিতা করতে গিয়ে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। শুধু জার্মানদের তরফ থেকে একই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে তারা অপারগ হয়নি, চেকদের বাধা দানেও তারা ছিল অক্ষম। সুতরাং ধীরে ধীরে হলেও প্রত্যয়ের সঙ্গেই তাদের পেছন দিকে ঠেলে দেওয়া হয়; একদিকে যেমন রাজনীতির জন্যে ধর্মের বিকৃতি, অপরদিকে তেমনি সফল বিরোধীতা। ছোটখাট সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে এটাই ছিল পদ্ধতি, বড় বড় সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রেও এ একই পদ্ধতি কাজ করছিল।
হাবুসবুর্গ যে জার্মান বিরোধিতা করে চলছিল যাজকদের সাহায্যে, সেই বিরোধিতাকে অধিকতর বলিষ্ঠ কোন বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। সুতরাং জার্মান প্রতিপত্তি ধর্মীয় দিক থেকে ধীরে ধীরে কমে আসে। সাধারণের ধারণা যে ক্যাথলিক চার্চ বিপুলভাবে জার্মান জনসাধারণকে অবহেলা করে চলেছে।
ওপর থেকে মনে হচ্ছিল যে ক্যাথলিক চার্চ জার্মানদের একেবারেই দেখছে না, বিরুদ্ধ পক্ষও এ মতবাদের প্রচারে সমর্থন করে এসেছে। এ শয়তানির শিকড় হল শ্ৰোয়েনারের মতে, ক্যাথলিক চার্চের নেতৃত্ব জার্মানিতে ছিল না, এবং একটা কারণই যথেষ্ট যে আমাদের লোকেরা চার্চের শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠে।
তথাকথিত সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলো পাদ প্রদীপের আড়ালে চলে গিয়েছিল। শুধু সাংস্কৃতিক সমস্যা কেন, সব সমস্যাগুলোরই এক গতি হয়েছিল। ক্যাথলিক চার্চের প্রতি প্যান্-জার্মান আন্দোলনের মৌলিক অধিকার ঠেলে পেছনে ফেলে দিয়েছে।
জর্জ শ্ৰোয়েনার যে কাজ ধরত তা অর্ধেক করে থেমে পড়ার মানুষ ছিল না। সে চার্চের বিরুদ্ধে মরণপণ যুদ্ধে নামে, কারণ তার ধারণা ছিল যে একমাত্র এ পথেই জার্মানদের রক্ষা করা সম্ভব। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে রোম থেকে সরে আসার আন্দোলন জোরদার করা হয়েছিল; কিন্তু এ পদ্ধতিতে বিরুদ্ধপক্ষের দুর্গ ধুলিসাৎ করা শুধু কষ্টকর নয়, অসম্ভবও বটে। শ্ৰোয়েনার বিশ্বাস করত যে যদি এ আন্দোলনকে সার্থকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, তবে এ যে জার্মানিতে দুটো বিরাট ধর্মীয় সম্প্রদায় দু’টুকরো হয়ে গেছে, তাকে রোধ করে যে বিশাল অন্তনিহিত শক্তির উৎপত্তি হবে, তার দ্বারা জার্মান সাম্রাজ্য এবং জাতিকে যে অতিশয় সমৃদ্ধ করা যাবে; শুধু তাই নয়, একেবারে বিজয়ের তোরণদ্বারে নিয়ে গিয়ে হাজির করা সম্ভব।
কিন্তু এ ব্যাপারটার শুরু এবং শেষ, দু’দিকই ভুলে ভর্তি ছিল।
এ বিষয়ে সন্দেহ নেই, জার্মানদের সম্পর্কে যে কোন বিষয়ে জার্মান পাদ্রীদের প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্যদের থেকে অনেক কম ছিল; বিশেষ করে চেদের সঙ্গে বুঝবার ক্ষমতা তো ওদের ছিল না বললেই চলে। একমাত্র কোন অজ্ঞ ব্যক্তিরই বোধ হয় অজ্ঞাত ছিল যে জার্মানির স্বার্থরক্ষার জন্য জার্মান পাদ্রীরা কোনরকম চেষ্টাই করেনি।
কিন্তু এ সঙ্গে যারা একেবারে অন্ধ নয়, তারা স্বীকার করবে যে আমাদের চারিত্রিক দোষেই আমরা প্রায় ধ্বংস হতে চলেছি। এ চরিত্রের জন্য আমরা আমাদের জাতিকে শ্রদ্ধা জানাতে কার্পণ্য করছি, জাতিকে শ্রদ্ধা দেখানো যেন এমন একটা জিনিস যেটা আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। চেক পত্নীরা অবশ্য নিজেদের লোক সম্পর্কে অন্তমুখী আর নিজেদের জাত সম্পর্কে বহির্মুখী। দুঃখের বিষয় আমাদের ক্ষেত্রে খুব কম করে হাজারটা বিষয়ে এ একই জিনিস দেখা যাবে।
এটা কোন রকমেই ক্যাথলিক ধর্মের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া নয়; এ জিনিসের উৎপত্তি আমাদের ভেতরেই যা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের সারবস্তুকে কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছে; বিশেষ করে সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে, যাদের নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্য আছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় আমাদের সরকারি অফিসাররা জাতির পুনরুত্থানের যে চেষ্টা করেছিল তার সঙ্গে যদি তুলনা করা হয়, অন্য জাতের সরকারি অফিসাররা এসব ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেশি প্রচেষ্টা নিশ্চয়ই দেখাত না। অথবা, আরো স্পষ্ট ভাষায় বলা যেতে পারে, অন্য কোন জাতির ক্ষেত্রে জাতীয় উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য সামরিক অফিসারবৃন্দ একইরকমভাবে পাশে এসে দাঁড়াত না। বরং ‘প্রদেশের শাসক’ বলে তার দায়িত্ব থেকে পালিয়ে বেড়া, যা আমাদের দেশে গত পাঁচবছর হয়েছে এবং এ ধরনের পুরস্কারের যোগ্য কোন যোগ্যতাই তারা দেখাত না। অথবা আমরা যদি আরেকটা উদাহরণ ধরি, ইহুদী সমস্যা সম্পর্কে দুই দৃষ্টিহীন ধর্মীয় সম্প্রদায় যে ধরনের মতবাদ পোষণ কত তা কি আজকের জাতির পক্ষে অত্যাবশ্যক, নাকি ধর্মের স্বার্থে? ইহুদী পুরোহিতদের যে কোন ব্যাপার যদি বিবেচনা করা যায়, এমনকি ইহুদী জাত সম্পর্কে সাধারণ একটা ব্যাপার—তাহলে তাদের মনোভাব এবং আমাদের গরিষ্ঠ জার্মান পাদ্রীদের মতবাদে কত ফারাক; তা ক্যাথলিক বা প্রটেস্টান্ট যাই হোক না কেন।
সমস্ত বিমূর্ত ব্যাপারেই আমরা এ একই ধরনের মতবাদে বিশ্বাসী।
‘দেশের শাসকবৃন্দ’ ‘গণতন্ত্র’, বিশ্বজনীন শান্তিবাদ, আন্তর্জাতিক একতা ইত্যাদি ধারণাগুলো যেন দৃঢ়, প্রামাণিক হয়ে দাঁড়ায় আমাদের কাছে, এবং জাতির জন্য সত্যিকারের যা প্রয়োজনীয় সেগুলোও যেন একান্তভাবেই এ আলোতে বিচার করা হয়ে থাকে।
এ যে জাতির প্রয়োজনীয় সবকিছুকে আগের ধারণা নিয়ে দেখার মজ্জাগত অভ্যাস আমাদের দাঁড়িয়ে যায়, যাতে সবকিছুকে আমরা বাঁকাভাবে দেখতে শুরু করি, সোজাসুজি কিছুই যেন আর নজরে আসে না। যেটা নিজেদের মতবাদেরই পরিপন্থী। শেষে পুরো ব্যাপারটাই নিজেদের কাছে ফিরে আসে। জাতির কোনরকম উন্নতির চেষ্টা করলেই অপকারি দলটা তাদের ছুঁড়ে ফেলে দেবে। কারণ এ ধরনের যে কোন প্রচেষ্টাকেই শাসনের অন্তরায় বলে ধরে নেওয়া হয়। শাসনের অন্তরায় বলে যারা ভাবে, তাদের চোখে শাসন মানে সেবা নয়, তারা হল প্রামাণিক কর্মকাণ্ডতে বিশ্বাসী, এবং সে তার নিজের দুর্দশার জন্য ক্ষমার যোগ্য। যদি কেউ একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চেষ্টামাত্রও করে, তবে তারা সঙ্গে সঙ্গে হৈ চৈ আরম্ভ করে দেয়। যদি সে ব্যক্তি ফ্রেডারিক দ্য গ্রেটও হয়। এমনকি সংসদে যারা সংসদীয় গণতন্ত্র করেছে, তারা যদি সংখ্যায় লঘিষ্ট এবং অক্ষমও হয়, অথবা বুদ্ধিমত্তার একেবারে নিচের স্তরে থাকে, তবু হৈ চৈ করতে কসুর করে না। কারণ এসব নিয়মবাদীদের কাছে গণতন্ত্রের আদর্শ জাতির আদর্শের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান। তার আদর্শ অনুসারে এসব দ্র সম্প্রদায়রা অত্যন্ত নিপীড়িত হয়ে ধ্বংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেও এ তথাকথিত শাসনের সমর্থন করে চলবে, অপরদিকে উপকারি সরকার হলেও তাকে অগ্রাহ্য করবে, কারণ সেটা যে তার ধারণার ‘গণতন্ত্র’ নয়।
একই উপায়ে জার্মান শান্তিবাদীর দল নিপ থাকছে যখন জাতি যন্ত্রণায় এবং উৎপীড়নে গভীর আর্তনাদ করছে। আর যখন পুরো দেশ প্রতিবাদের জন্য উন্মুখ। কিন্তু এ প্রতিবাদের অর্থ হল সামরিক শক্তি প্রয়োগ, যা হল শান্তিবাদীদের আদর্শের বিরুদ্ধে।
আন্তর্জাতিক জার্মান সোশ্যালিস্টদের পৃথিবীর অন্য সব দেশের সহকর্মীরা একতার নামে প্রতারণা এবং লুণ্ঠন করতে পারে; কিন্তু তারা সবসময়ই তাদের ভ্রাতৃবৎ দেখে এসেছে, এবং কখনই তাদের ফিরতি প্রতারণা বা লুণ্ঠন করতে চায়নি। এমনকি নিজেদের আত্মরক্ষা পর্যন্ত করেনি। কিন্তু কেন? কারণ সে হল–জার্মান।
এ ধরনের সত্যকে হয়ত বা মেনে নেওয়া ঠিক নয়; কিন্তু কিছু যদি পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে তবে তা আমাদের প্রথমে রোগটা সঠিকভাবে নির্ণয় করা উচিত।
যে ব্যাপারটা আমি এইমাত্র ব্যক্ত করলাম, সেটা প্রমাণ করে যে জার্মান পাদ্রীদের একাংশ কত দুর্বলভাবে জার্মানদের স্বার্থ দেখত।
আমাদের জাতীয় চরিত্রে এ দৃঢ়তা এবং স্থিরতার অভাবের কারণ হল আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি। আমাদের যুবকদের জার্মান জাতিকে উপযুক্ত করার চেয়ে এ শিক্ষার উদ্দেশ্য যেন ওদের আদর্শের কাছে অসহায় করে তোলে। আদর্শ যেন একটা প্রতিমূর্তি।
যে শিক্ষা পদ্ধতি তাদের কতগুলো ধারণার ভক্ত করে তোলে, যেমন গণতন্ত্র, আন্তর্জাতিক সোশ্যালিজম, শান্তিবাদী ইত্যাদি ধ্যান-ধারণাগুলো বাইরে থেকে তাদের এমনভাবে গড়ে যে জীবনের মূল উদ্দেশ্য যেন এ ধারণাগুলোকেই রূপ দেওয়া। কিন্তু অপরদিকে নিজের জাত জার্মানদের সম্পর্কে ছোটবেলা থেকেই একটা অনীহার ভাব গড়ে ওঠে। শান্তিবাদী যারা জার্মান তারা দেহমন ছোটবেলা থেকেই গোঁড়া আদর্শের কাছে বিকিয়ে দিয়ে বসে থাকে; যখনই বিপদজনক কোন অবস্থার মুখোমুখি জাতি এসে দাঁড়ায়, তখন এরা বিচার করতে বসে কোনটা ঠিক আর কোনটা ঠিক নয়। এমনকি এ বিপদ যদি মারাত্মক এবং প্রায় ধ্বংসের কাছেও জাতিকে নিয়ে যায়, তবু সে নিজের লোকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সংগ্রামে নামবে না; এমনকি নিজেদের আত্মরক্ষার প্রশ্নেও নয়।
বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের ওপর কি ধরনের প্রতিক্রিয়া ঘটে তার আরেকটা উদাহরণ দেওয়া যায়। যখন বংশ পরম্পরায় জার্মান আদর্শ হয়, প্রটেস্টান্ট ধর্মমতের লোকেরা তাদের আদর্শকে আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরে। কিন্তু জাতীয় স্বার্থের বেলায় এরাই সবচেয়ে আগে সরে দাঁড়ায়। কারণ এটা ধর্মের আদর্শ বা বংশ পরম্পরায় কোন ব্যাপার নয়, কোন একটা কারণ দেখিয়ে তা বাতিল করে দেবে।
সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রটেস্টান্টরা নৈতিক সাধুতা বা জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতির ভাষা বা আধ্যাত্মিক ব্যাপারে নিজেদের রক্ষা করার জন্য মনপ্রাণ সঁপে দেবে; কারণ এগুলোই যে ওদের ধর্মীয় আদর্শ যার জন্য তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু এ প্রটেস্টান্টরাই জাতি যখন শত্রুর আক্রমণের মুখোমুখি, তা থেকে উদ্ধারের প্রতিটি প্রচেষ্টাকে তারা প্রাণপণে বাধা দেবে। কারণ ইহুদীদের প্রতি এদের ধারণা দৃঢ় এবং গোড়াভাবে স্থির। যদিও এটাই হল প্রথম সমস্যা যার সমাধানের প্রয়োজন, এবং জার্মান জাতির এ চরম অধঃপতনের থেকে পুনরুত্থানের পথে টেনে ওঠানো এ সমস্যার সমাধান ছাড়া অসম্ভব।
ভিয়েনার প্রবাসী দিনগুলোয় আমার প্রচুর অবসর এবং সুযোগ ছিল কোনরকম সংস্কার ছাড়াই সমস্যাটাকে বিশ্লেষণ করার এবং প্রত্যহ যে হাজার হাজার লোকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হত, তার থেকে আমার সমাধান যে নির্ভুল এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছিলাম।
এ আলোতেই যেখানে অনেক জাতির লোক এক বিন্দুতে এসে মিলেছে, তাদের কাছে এটা দিনের আলোর মত স্পষ্ট যে জার্মান শক্তিবাদীর দল তাদের জাতির স্বার্থের ওপরই দেখেছে। উপরন্তু আমি দেখেছি জার্মান সোশ্যালিস্টরা একমাত্র আন্তর্জাতিকতাবাদী এবং জাতির স্বার্থের ব্যাপারে কোন রকম দাবি দাওয়াই তাদের নেই; একমাত্র অন্য দেশের সহকর্মীদের কাছে বিলাপ করা ছাড়া। কেউ কিন্তু চেক্ বা পোলিশদের চরিত্রে এ কলঙ্ক আরোপ করতে পারবে না। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে, চরিত্রের এ কলঙ্কময় দিকটার জন্য দায়ী সেই দিনের মতবাদ। পুরোপুরি দায়িত্ব হল শিক্ষা ব্যবস্থার; যেটা আমাদের জাতীয় আদর্শকে কখনই গড়তে দেয়নি।
সুতরাং প্যান-জার্মান আন্দোলনের নেতাদের ক্যাথলিক ধর্মমতের বিরোধিতা আমার মতে পুরোপুরি অসমর্থনীয়।
একমাত্র এ শয়তানির সমাধানের উপায় হল, জার্মান যুবকদের ছোটবেলা থেকে মনটাকে বিষিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে কি করে স্বার্থরক্ষা করতে হয়, সেই বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া। যখন তারা অত্যন্ত ছোট, তখন থেকেই প্রত্যেকটা বস্তুকে ওপর থেকে দেখার প্রবণতা তাদের ভেতরে প্রবেশ করে, যেটা ভবিষ্যতে আমাদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে ফেলে। এর ফলে আয়ারল্যান্ড, পোল্যান্ড কিংবা ফ্রান্সের মত ক্যাথলিকরা প্রথমে এবং সর্বাগ্রে হবে জার্মান। কিন্তু এ যে আগে থেকে শিক্ষা তা সরকারের একটা মৌলিক পরিবর্তন আনতে সমর্থ হবে।
আমার এ মতবাদের সবচেয়ে জোরাল সমর্থন হল, ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে যখন শেষবারের মত ইতিহাসের বিচারশালায় আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য গিয়ে দাঁড়াতে হয়েছিল, সে ছিল জীবন মরণের সংগ্রাম।
যতদিন পর্যন্ত ওপরের নেতৃত্বের অভাব ছিল না, জনসাধারণ তাদের কর্তব্য যতটা সম্ভব বেশি পরিমাণেই পালন করেছে। তা সে প্রটেস্টান্ট ধর্মযাজক বা ক্যাথলিক পাদ্রী, যে-ই হোক না কেন, চেষ্টা করেছে আপ্রাণ তা তুলে ধরতে শুধু বাইরের জীবনেই নয়, দৈনন্দিন জীবনেও। বিশেষ করে উৎসাহের প্রথম জোয়ারের সময়। উভয় ধর্মই পবিত্র জার্মান সাম্রাজ্যকে ভাগাভাগি করা হয়নি, যা রক্ষা এবং ভবিষ্যত সমৃদ্ধির জন্য তারা ঈশ্বরের কাছে সতত প্রার্থনা করেছে।
অস্ট্রিয়ার প্যান-জার্মান আন্দোলনের নেতাদের নিজেদেরই একটা প্রশ্ন করা উচিত, যতদিন পর্যন্ত তাদের বিশ্বাস ক্যাথলিক ধর্মে আছে, ততদিন পর্যন্ত অস্ট্রিয়াতে এ জার্মানিদের থাকতে দেওয়া উচিত কিনা? যদি এ প্রশ্নের উত্তর ইতিবাচক হয়, তবে রাজনৈতিক দল হিসেবে এর ধর্মীয় দলাদলিতে জড়িয়ে পড়াটা উচিত হয়নি। কিন্তু উত্তরটা যদি নেতিবাচক হয়, তবে এদের ধর্মীয় সংস্কারে নামা উচিত ছিল; রাজনৈতিক আন্দোলনে নয়।
যারা বিশ্বাস করে যে রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে ধর্মীয় সংস্কার সম্ভব, তাদের শুধু ধর্ম নয়, কোন মতবাদে বিশ্বাস এবং বাস্তবে চার্চের কি প্রতিক্রিয়া—এসব সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই।
কোন মানুষের পক্ষে দু’জন প্রভুকে সেবা করা সম্ভব নয় এবং ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি যে ধর্মের ভিত্তিভূমি উপড়ে ফেরার চেয়ে কোন দেশের সরকার উপড়ে ফেলা
অনেক সহজ। সত্যি বলতে কি, একটা দলের পক্ষে এটা বিশেষ কিছু কাজ নয়।
এর বিরুদ্ধে কোন যুক্তিই খাটে না। বরং বলা যায় আক্রমণটা করা হয়েছিল আত্মরক্ষার খাতিরে, কোন বহিরাক্রমণ রুখবার জন্য নয়।
সন্দেহ নেই যে সব সময়েই কিছুসংখ্যক নীতিজ্ঞান শূন্য দুরাত্মা থাকে, যারা রাজনীতির পটভূমি হিসেবে ব্যবহারের জন্য ধর্মকে টেনে নিচে নামিয়ে নিয়ে আসে। প্রায় সব সময়েই এদের মনে ধর্ম এবং রাজনীতি নিয়ে ব্যবসা করার ধান্দা থাকে। কিন্তু এরজন্য চার্চকে দোষারোপ করা অন্যায়; কারণ সর্বদাই এ সংসারে কিছু দূরাত্মা থাকে, তারা যারই সংস্পর্শে আসে তাকেই প্রতারণা করে। তার জন্য ধর্ম বা কোন ধার্মিক সম্প্রদায়কে দোষী বা দায়ী করা যায় না।
এ সংসদীয় কুঁড়ে এবং প্রবঞ্চকদের কাছে কোন একটা বলির ছাগল খোজার চেয়ে সুস্বাদু বস্তু আর কিছু নেই; অবশ্যই ঘটনা ঘটে যাবার পর। যে মুহূর্তে ধর্ম বা ধর্মীয় কোন সম্প্রদায়কে এর জন্য আক্রমণ করা হয়, সেই মুহূর্তে সে এবং তার ভ্রষ্ট দল হৈহুল্লা চিৎকার জুড়ে দিয়ে সারা পৃথিবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং বোঝাতে চেষ্টা করে সে এবং তার সৃষ্ট গোলমালই একমাত্র চার্চ এবং ধর্মকে রক্ষা করেছে। জনসাধারণ স্বভাবতই বোকা এবং স্মৃতিশক্তি না থাকায় মনে করতে পারে না যে এ গোলমালের পেছনে চাবিকাঠি কে নাড়ছে এবং কার জন্য এ হাঙ্গামা। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই গোলমালটা কে শুরু করেছিল ভুলে যাওয়াতে এ প্রবঞ্চকগুলো সহজে রেহাই পেয়ে যায়।
ধূর্তেরা সব সময়ই জানে তার কুকাজের সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। সুতরাং যখন সে দেখে সৎ অথচ কৌশলহীন প্রতিপক্ষ হেরে গেছে, তখন সে জামার অস্তিন গুটিয়ে নিয়ে আরো বেশি হাসতে শুরু করে এবং তার প্রতিপক্ষ একসময় জনসাধারণের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে ফেলে জনজীবনের কোন ব্যাপারে অংশগ্রহণের থেকে অবসর নেয়।
কোন একক ব্যক্তির কুকার্যের জন্য চার্চ বা ধর্মকে দায়ী করা আরেকটা দৃষ্টিকোণ থেকেও অন্যায়। কেউ যদি দলের বিশালত্ব তুলনা করে, যেটা সাদা চোখে সবাই দেখতে সক্ষম, তাহলে মানব চরিত্রের সাধারণ দুর্বলতাগুলো মেনে নিয়েও আমাদের স্বীকার করা উচিত যে খারাপের চেয়ে ভালর দিকের পাল্লাই এখানে বেশি ভারী। পাদ্রীদের মধ্যেও কয়েকজন থাকতে পারে যারা তাদের পবিত্র আহ্বান রাজনৈতিক উচ্চাশা পূরণের কাজে লাগায়। দুর্ভাগ্যবশত কিছু ধর্মযাজক ভুলে যায় এ রাজনৈতিক দাঙ্গায় তাদের আরো বেশি বিশ্বস্ত যোদ্ধা হওয়া উচিত। মিথ্যা এবং দুষ্কর্মেরতদের সাহায্যকারী হিসেবে কোন কাজ করা তাদের পক্ষে অন্যায়। তবে প্রতিটি অন্যায়কারীর তুলনায় আরো হাজার ধর্মযাজক আছে, যারা এ পংকিল সমুদ্রের মধ্যে ছোট ছোট দ্বীপের মত মাথা উঁচু করে নিজেদের ধর্মীয় কাজ অতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছে।
আমার পক্ষে চার্চকে দোষী করা সম্ভব নয়, তার স্বপক্ষে যথেষ্ট কারণও নেই। যদি কিছু ভ্রষ্ট ব্যক্তি পাদ্রীর পোশাক পরে নৈতিক আইন কানুনের বিরুদ্ধে কোনকিছু করে, তবু মুহূর্তের জন্যও আমি চার্চকে দোষারোপ করব না। চার্চের অগুন্তি সভ্যদের মধ্যে কয়েকজন হয়ত বা তাদের স্বদেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। কারণ এ যুগে তো সেটা খুব সাধারণ ব্যাপার। বিশেষ করে আমাদের যুগে ভোলা উচিত নয় যে গ্রীক বিশ্বাসঘাতক ফিলটেসের* সময়েও হাজার লোক বর্তমান ছিল যাদের হৃদয়ে তাদের স্বদেশবাসীর দুঃখে সবসময়ে রক্তক্ষরণ হত। তাই আমাদের দুর্ভাগ্যের কালো ছায়া সরে গিয়ে যখন সুখের সূর্য মুখ বাড়াবে, তখন এরাই জাতির মুকুট হিসেবে বিবেচিত হবে।
এখানে যদি এ প্রশ্ন কেউ তোলে যে আমরা দৈনন্দিন ছোট ছোট সমস্যাগুলোর আলোচনা করছি না, কিন্তু ধর্মের ব্যাখ্যা করে চলেছি, তবে তার একমাত্র উত্তর হল:
তুমি কি মনে কর সময় তোমাকে পৃথিবীতে সত্য স্থাপনের জন্য আহ্বান করেছে? তাই যদি হয়, তবে তাই কর। কিন্তু সে কাজ প্রত্যক্ষভাবে করার মত সাহস তোমার থাকা চাই এবং কোন রাজনৈতিক দলকে মুখবন্ধ হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ এ উপায়ে তুমি তোমার বৃত্তিকেই ত্যাগ করবে। বর্তমানে যার অস্তিত্ব আছে তাকে আরো ভাল কিছু করা উচিত যা ভবিষ্যতেও টিকে থাকবে।
যদি তোমার সে রকম সাহস না থাকে বা এর পরিবর্তে সঠিক জিনিসটা কি হবে জানা না থাকে, তবে সেটাকে আগের মতই থাকতে দাও। নাড়াচাড়া করাটা ঠিক হবে না। কিন্তু যা-ই ঘটে থাকুক না কেন, রাজনৈতিক দলের স্বার্থে ঘোরাপথে নিজের উদ্দেশ্য সাধন করতে যেও না, যদি তোমার মুখোশ খুলে সংগ্রাম করার মত সৎসাহস না থাকে।
রাজনৈতিক দলগুলোর ধর্মের ব্যাপারে অযথা হস্তক্ষেপ করার কোন অধিকারই নেই, যদি না তার সঙ্গে জাতির স্বার্থের প্রশ্ন জড়িত থাকে। কারণ তা সমগ্র জাতিকে সংস্কৃতি, নৈতিকতা প্রভৃতি সবদিক থেকে টেনে নিচে নামিয়ে নিয়ে যাবে।
যদি কোন উচ্চ পদস্থ যাজক ধর্মীয় উৎসব বা কুশিক্ষা ব্যবহার করে যা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী তবু তার প্রতিপক্ষের সেই রাস্তাতে যাওয়া উচিত নয় বা একই অস্ত্রে যুদ্ধ করাটাও ঠিক হবে না।
কোন রাজনৈতিক নেতার কাছে যদি ধর্মীয় অনুশাসন এবং তার প্রচার পবিত্র এবং অলঙ্খনীয় বলে বিবেচিত হয়, তবে তাকে কোনরকমেই রাজনৈতিক নেতা বলা চলে না। সে হল ধর্ম সংস্কারক। যদি অবশ্য তার ধর্ম সংস্কারের জন্য প্রয়োজনীয় গুণগুলো থাকে।
.
প্যান-জার্মান আন্দোলন এবং তাদের রোমের সঙ্গে বিরোধ নিয়ে আমি স্থির নিশ্চিত যে, বিশেষ করে শেষের দিকে প্যান-জার্মান আন্দোলনকারীরা সামাজিক সমস্যাগুলো থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নেওয়ার ফলে জনসাধারণের সমর্থনও হারিয়ে ফেলে, যারা হল এ ধরনের সংগ্রামের অতি নির্ভরযোগ্য যোদ্ধা। সংসদে প্রবেশ করে প্যান-জার্মান আন্দোলনকারীরা নিজেদের ভেতরের শক্তিটাকে হারায়, যার উৎসস্থল হল জনসাধারণ এবং সংসদের পরাজয়ের বোঝাটাকেও তাদের ঘাড়ে এসে পড়ে। চার্চের সঙ্গে তাদের রেষারেষির দরুন, নিচু এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসংখ্য জনসাধারণের আস্থা তারা হারিয়ে ফেলে; ওপরের স্তরেরও অনেকে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে যাদের অনেককেই জাতির মূল্যবান সম্পদ হিসেবে গণ্য করা চলে। সুতরাং অস্ট্রিয়ার সংস্কৃতি আন্দোলনের হিসেবের খাতায় লাভের পরিবর্তে ঢ্যাড়াই পড়ে।
যদিও তারা দশ লাখ লোককে চার্চের আওতা থেকে ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিল, তবু তাতে পরবর্তীদের কোন ক্ষতি হয়নি। কারণ চার্চের পক্ষে হারানো মেষগুলোর জন্য চোখের পানি ফেলার কোন মানে হয় না। এরা হৃদয় দিয়ে চার্চকে কোনদিন ভালবাসেনি। এ নতুন সংস্কারের সঙ্গে মহাসংস্কারের পার্থক্য এ যে মহাসংস্কার কালের একটা বিখ্যাত ঘটনা, যখন চার্চ ধর্মের জন্য তার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারায়। কিন্তু এ নতুন সংস্কারে তারাই একমাত্র চার্চ ছেড়ে বেরিয়ে আসে যাদের সঙ্গে চার্চের যোগাযোগ আগেও নিবিড় ছিল না। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটাকে শুধু হাস্যাস্পদ ঘটনাই বলা চলে না, শোচনীয়ও বটে। আরো একবার জার্মান জাতির পক্ষে প্রতিশ্রুতিময় একটা রাজনৈতিক আন্দোলন যা ব্যর্থ হয়। কারণ এটাকে রূঢ় বাস্তবের প্রতি অবিচলিত অনুরাগ রেখে পরিচালিত হয়নি। তাই এমন একটা জায়গায় আন্দোলনের স্রোত গিয়ে পড়ে যেখানে আপনা থেকেই তা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়তে বাধ্য।
যদি বিশাল জনসাধারণের মনস্তত্ত্ব বুঝতে পারত তবে প্যান-জার্মান আন্দোলন নিশ্চয়ই এ ভুল করত না। নেতাদের যদি এটা জানা থাকত তবে একমাত্র মনস্তাত্ত্বিক
কারণেই জনসাধারণের সামনে একটার বেশি দুটো প্রতিদ্বন্দ্বী খাড়া হতে দিত না, কারণ এটা তাদের সগ্রাম করার শক্তিটাকেই টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল। তাদের উচিত ছিল পূর্ণশক্তি নিয়ে একক প্রতিদ্বন্দ্বীর সামনে দাঁড়ানো। একটা রাজনৈতিক দলের নীতির পক্ষে এটা বিপজ্জনক, যা কিনা এমন একজন মানুষের দ্বারা পরিচালিত যে তার আঙুল প্রতিটি মটর দানার ওপর রাখতে চায়, কিন্তু সহজ একটা ব্যঞ্জন রান্না করাও তার পক্ষে সম্ভব নয়।
বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের বিপক্ষে কথা বলা যেতে পারে এমন অনেক কিছুই আছে, তবু রাজনৈতিক নেতাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে ইতিহাসের শিক্ষা কোন নির্ভেজাল রাজনৈতিক দল এ পরিবেশে ও পরিস্থিতিতে ধর্মের সংস্কার করতে সক্ষম হয়নি। কেউ ইতিহাস পড়ে না শিক্ষাকে অবিশ্বাস করতে বা ভুলে যাওয়ার জন্য, যখন সত্যিকারের সময় উপস্থিত হয় তা বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য। এ বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্যরকম হয়েছিল এ ধারণা করাটা ভুল হবে, যেখানে ইতিহাসের অনন্তকালের সত্যটা ঠিক খাটে না। কেউ ইতিহাসের শিক্ষা নেয় বর্তমানে সেটা প্রয়োগের উদ্দেশ্যে, যে সেটা করে না, তার কোন যোগ্যতাই নেই। বাস্তবে তার জ্ঞান তাহলে ব্যাপারটায় ভাসা ভাসা অথবা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই যা হয়ে থাকে, সে একটি দাম্ভিক কিন্তু সহজে প্রতারিত হয় এমন নির্বোধ ব্যক্তি যার সৎ উদ্দেশ্য তার বাস্তব ব্যাপারে অক্ষমতার পরিপূরক নয়।
নেতৃত্বের কৌশল, যা নাকি বিরাট বিরাট নেতারা যুগে যুগে করে এসেছে, তা হল সমস্ত জনসাধারণের মনোযোগ একত্রিত করেছে মাত্র একজন প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে এবং সতর্কতা নিয়েছে যাতে কোন রকমেই সেই মনোযোগী জনসাধারণ ভেঙে টুকরো টুকরো
হয়। যত বেশি জনসাধারণের যুদ্ধরত শক্তি একটা দৃশ্যের ওপর পড়বে, তত বেশি নবাগত সেই আন্দোলনে যোগ দেবে তার চৌম্বক শক্তিতে আকৃষ্ট হয়ে যার দ্বারা সেই আন্দোলনের তীব্রতা অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে। প্রতিভাধর নেতাদের এমন ক্ষমতা থাকা উচিত যাতে নাকি তারা অনেক বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদেরও একই ধরনের বিরোধিতা বলে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে পারে; দুর্বল এবং টলমলে চরিত্রের নেতাদের নিজেদের কাজ সম্পর্কে সন্ধিগ্ধ মনোভাব নিজেদের ভেতরে গড়ে উঠবে, যদি তাদের অনেকগুলো বিভিন্ন ধরনের শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়।
যে মুহূর্তে অস্থির জনসাধারণ দেখতে পাবে তাদের প্রতিপক্ষ রকমারী দলের সংমিশ্রণে তৈরি, তখনই তারা মনে করবে যে এটা কি রকম হল? আমরা এবং আমাদের আন্দোলনই একমাত্র সঠিক। আর প্রতিপক্ষের মত এবং আদর্শ ভুল।
এ ধরনের অনুভূতি প্রথমেই তাদের সংগ্রাম করার শক্তিটাকে পঙ্গু করে দেবে, যেখানে বিভিন্ন ধরনের শত্রুতা একই কেন্দ্র থেকে ছিটকে বেরিয়েছে। তাদের এক জায়গায় আটকে একটা প্রতিপক্ষের সৃষ্টি করতে হবে, যাতে সংগ্রামরত জনসাধারণ তাদের সামনে একজন প্রতিপক্ষকেই দেখতে পায়; যার বিরুদ্ধে তাদের লড়তে হবে। এ ধরনের একতা তাদের নিজেদের বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করবে এবং প্রতিপক্ষের প্রতি বিরোধিতার অনুভূতিটা চরমে নিয়ে যাবে।
প্যান্-জার্মান আন্দোলনের ব্যর্থতার জন্য দায়ী হল এর নেতারা, যারা এ সত্যের রহস্যটা অনুধাবন করতে পারেনি। তারা তাদের লক্ষ্যটাকে স্পষ্ট দেখেছিল এবং ভেবেছিল তাদের নীতিটাই সঠিক; কিন্তু এ ধারণার বশবর্তী হয়েই তারা ভুল রাস্তায় গিয়ে পড়েছিল। এদের কার্যকলাপের সঙ্গে তুলনা করা চলে সেই আলপস পর্বতে আরোহণকারী, যে চূড়ার দিকেই দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে পথ এগোচ্ছিল, যার দৃঢ়তা এবং শক্তি ছিল শ্রেষ্ঠত্বের তুঙ্গে, কিন্তু পায়ের নিচেকার রাস্তাটাকেই সে দেখেনি। তার দৃষ্টি উদ্দেশ্যের প্রতি এতই নিবদ্ধ ছিল যে সে আরোহণের পথটা নিয়ে চিন্তা করেনি বা তাকিয়েও দেখেনি; তাই শেষে তাকে বাধ্য হয়ে পরাজয় বরণ করে নিতে হয়েছে।
প্যান্-জার্মান পার্টির প্রতিদ্বন্দ্বী তাদের লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য যে রাস্তা বেছে নিয়েছিল তা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এদের নির্বাচিত রাস্তা শঠতার। কিন্তু এদের উদ্দেশ্যে পৌঁছবার জন্যে ধ্যান-ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট ছিল না। যেসব কারণে প্যান-জার্মান আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল, সেই সব নীতি সম্পর্কে খ্রিস্টান সোশ্যালিস্ট পার্টি ছিল সঠিক এবং নিয়মতান্ত্রিক।
তারা জনসাধারণের গুরুত্ব ঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিল এবং প্রথম থেকেই আন্দোলনের সামাজিক চরিত্রটার দিকে নজর দেওয়ায় বিপুল জনতার জনপ্রিয়তা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। বিশেষ করে নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং শ্রমশিল্পীদের প্রতি আবেদন রাখায় তাদের সমর্থন পেয়েছিল–যারা বিশ্বাসী, ধৈর্যশীল এবং আত্মোৎসর্গকারী। খ্রিস্টান সোশ্যালিস্ট পার্টির নেতারা প্রথম থেকেই অতি সতর্কভাবে ক্যাথলিক ধর্ম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে হৃদ্য সম্পর্ক বজায় রাখায় এ বিশাল প্রতিষ্ঠানের পুরো সমর্থন পেয়েছিল। এ আন্দোলনের নেতারা বিরাটভাবে প্রচার ব্যবস্থায় বিশ্বাস করত এবং এরা প্রকৃতই ধার্মিক ছিল। যে কারণে বিশাল জনতার মধ্যে আধ্যাত্মিক একটা সহজাত প্রেরণা জাগাতে পেরে এরা তাদের সমর্থন লাভ করে।
এ পার্টির নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারার প্রধান দুটো কারণ ছিল, যে কারণদ্বয়ের জন্যে তাদের পক্ষে অস্ট্রিয়াকে শেষ পর্যন্ত বাঁচানো সম্ভব হয়নি।
খ্রিস্টান সোশ্যালিস্টদের ইহুদী বিদ্বেষের পটভূমি ধর্মীয় ভিত্তিতে ছিল, জাতি বিদ্বেষের আদর্শের ওপর নয়; এ ভুল থেকেই দ্বিতীয় ভুলের জন্ম হয়েছিল।
খ্রিস্টান সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতাদের ধারণা ছিল যদি অস্ট্রিয়াকে রক্ষা করতে হয় তবে তাদের ধ্যান-ধারণা জাতিগত হওয়া উচিত হবে না। কারণ তাদের মনে হয়েছিল এ ধরনের নীতি নিলে অস্ট্রিয়া টুকরো টুকরো হয়ে যাবে। পার্টির সর্বোচ্চ নেতার ধারণা ছিল যে ভিয়েনা টুকরো টুকরো হয়ে যেতে পারে এমন কোন ব্যাপার বা চিন্তাধারা সযত্নে পরিহার করা উচিত। এবং যে সব চিন্তাধারা রকমারী জাতিকে এক সুতোয় বাধতে পারবে, একমাত্র তাকেই উৎসাহ দেওয়া উচিত।
সে সময় ভিয়েনায় পরদেশীদের মধুচক্র ছিল, বিশেষ করে চেদের। এদের জার্মান বিরোধী নয় এমন কোন দলে তালিকাভুক্ত করতে সবিশেষ ধৈর্য্যের প্রয়োজন ছিল। অস্ট্রিয়াকে বাঁচাতে হলে ওদের অপরিহার্যতাকে স্বীকার করে নিতেই হয়। সুতরাং ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের সমর্থন পাওয়ার সবরকম চেষ্টাই করা হয়েছিল, যাদের বেশির ভাগই ছিল চে। যারা ম্যানচেষ্টার স্কুলের উদার আদর্শের তথাকথিত যোদ্ধা, তাদের বিশ্বাস এ ধরনের মতবাদের সাহায্যে তারা ইহুদীদের বিরোধিতা করতে সক্ষম হবে। কারণ ধর্মীয় অনুসন্ধানের জালে জড়িয়ে পড়ে অন্য ধর্মের লোকেরা একত্রিত হবে, যা পুরনো অস্ট্রিয়ার লোকসংখ্যার সমসংখ্যক।
এটা পরিষ্কার যে এ ধরনের ইহুদী বিদ্বেষ ইহুদীদের খুব একটা ভাবিয়ে তুলতে পারেনি। কারণ এটা পরিষ্কার ধর্মীয় ভিত্তিভূমিতে স্থাপিত। খুব বেশি খারাপ হলে তো দরকার মাত্র কয়েক ফোঁটা পবিত্র পানির, যা ছিটিয়ে দিলেই সমস্যা শেষ। তার পরেই নিশ্চিন্ত মনে যেমন ব্যবসাও করা যাবে আর তেমনি ইহুদী জাতীয়তা বজায় রাখা যাবে।
এসব ভাসা ভাসা কারণে সম্পূর্ণ সমস্যাটাকে সমাধান করার ব্যাপারে যুক্তিসংগতভাবে অসম্ভব ছিল। তার ফলে বহুলোকই ইহুদী বিদ্বেষী ব্যাপারটা পুরোপুরি অনুধাবন করতে না পেরে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণই করে না। আদর্শের চৌম্বক শক্তি এভাবে নিতান্ত একটা সংকীর্ণমনা দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কারণ নেতারা অনুভূতির আরো উচ্চস্তরে আরোহণে অসমর্থ হয়ে পড়ে এবং তার ভিত্তিভূমি সঠিক যুক্তিসঙ্গতভাবে স্থির করা হয় না। আদর্শগতভাবে বুদ্ধিমানেরা তাই এ নীতিকে সমর্থনও করে না। সমস্ত আন্দোলনটাকেই যেন মনে হচ্ছিল ইহুদীদের ধর্মান্তরকরণের একটা নতুন প্রচেষ্টা। অপরদিকে মনে হচ্ছিল এটাকে দলবদ্ধভাবে এ ধরনের আন্দোলনের আরো একটা প্রচেষ্টা। এভাবে সমগ্র সংগ্রামটাই তার আধ্যাত্মিক এবং ভক্তিসম উৎপাদক চরিত্রটা হারিয়ে বসে থাকে। সত্যি কথা বলতে কি, কিছু মানুষের চোখে, যাদের কোন রকমেই অপদার্থ বলা যায় না, পুরো আন্দোলনটাকেই আদর্শভ্রষ্ট এবং তিরস্কারের যোগ্য বলে মনে হয়। সুতরাং সমস্ত মানব জাতির পক্ষে ভীষণ প্রয়োজনীয় কোন সমস্যা বর্তমান, যার ওপরে ইহুদী ছাড়া পৃথিবীর অন্য সব জাতির অস্তিত্ব নির্ভর করছে—এ বিশ্বাস মানুষের মধ্যে জাগাতে ব্যর্থ হয়।
গয়ংগচ্ছভাবে নিয়ে পুরো সমস্যাটাকে সমাধানের প্রচেষ্টা খ্রিস্টান সোশ্যালিস্টদের বিদ্বেষী নীতিকে ভোঁতা করে দেয়।
এ আন্দোলনের বাইরের রূপটাই ছিল একমাত্র ইহুদী বিদ্বেষী। এবং এর ফলাফল অনেক দূর পর্যন্ত গড়ায়, তার চেয়ে সম্ভবত ইহুদী বিদ্বেষী ভাব আন্দোলনে না থাকলেই ভাল ছিল। কারণ এ ভুল ধারণা মানুষের মধ্যেও একটা ভুল ধারণার সৃষ্টি করেছিল যে শত্রুকে কান ধরে টানা হয়েছে; কিন্তু সত্যিকারের অবস্থা দেখতে গেলে দেখা যাবে, শত্রুকে কান ধরে টানার পরিবর্তে জনসাধারণকেই নাকে খত দিতে হয়েছে।
ইহুদীরা এ ইহুদী বিদ্বেষী পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেয় এবং দেখে যে এ ইহুদী বিদ্বেষী পরিবেশই তাদের পক্ষে লাভজনক। এ পরিবেশের অবলুপ্তি তাদের ক্ষতি ডেকে আনবে।
পুরো আন্দোলনটাই দেশের কাছে, যা অসদৃশ্য জাতির সমন্বয়ে গঠিত আরও বেশি আত্মোৎসর্গ কামনা করে, বিশেষ করে জার্মানদের অছিরূপে বেশি প্রয়োজন ছিল।
এমনকি ভিয়েনাতেও কেউ জাতীয়তাবাদী হতে সাহস করত না পায়ের তলায় মাটি সরে যাবার ভয়ে। হাবুসবুর্গ সরকারের ধারণা ছিল জাতীয়তাবাদী প্রশ্নটা চুপচাপ এড়িয়ে যেতে পারলেই বোধহয় হাবুবুর্গ সরকার রক্ষা পেয়ে যাবে। কিন্তু এ নীতি সরকারের ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসে এবং একই নীতি খ্রিস্টান সোশ্যালিজমের মৃত্যুও ঘনিয়ে আনে। এভাবে আন্দোলনটা যার থেকে একটা রাজনৈতিক দল তার প্রয়োজনীয় এগিয়ে যাবার শক্তি আহরণ করবে, সেই একমাত্র উৎসটাকেই হারিয়ে ফেলে।
এ বছরগুলোতে আমি উভয় আন্দোলনকেই সতর্কভাবে অনুধাবন করি। কেমন করে তারা উন্নতির ধাপে ধাপে এগোচ্ছিল। একটা আন্দোলনের সঙ্গে আমার হৃদয়ের যোগ ছিল, আর আরেকটার সঙ্গে এ বিস্মৃত মানুষটার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ছিল, যাকে আমার তখন মনে হয়েছিল অস্ট্রিয়ায় বসবাসকারী জার্মানদের শ্রেষ্ঠ প্রতীক।
যখন মৃত বুর্গার মাষ্টার বা মেয়রের শবযাত্রার মিছিলটা সিটি হল থেকে রি স্ট্রাসের দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, হাজার হাজার লোকের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমিও দেখেছিলাম সে পবিত্র নীরব শবযাত্রার মিছিলকে চলে যেতে। পুরো ব্যাপারটা যেন আমার মনটাকে সজোরে নাড়া দিয়ে যায় এবং আমার সহজাত প্রবৃত্তি যেন বলে দেয়, এ মানুষটার সমস্ত কাজই পণ্ডশ্রম হয়েছে। কারণ একটা অনমনীয় দানব ভাগ্য এ সরকারকে টেনে নিয়ে চলেছে পতনের দিকে। যদি ডক্টর লুইগের জার্মানিতে বসবাস করত, তবে আমাদের জনসাধারণের মধ্যে নেতৃত্বের পদ তাঁকে দেওয়া হত; এটা তারই দুর্ভাগ্য যে এমন একটা দেশে তাকে কাটাতে হয়েছে যেখানে তার করার কিছুই ছিল না।
তার মৃত্যুর পরেই বালাকান দেশসমূহে আগুন জ্বলে উঠেছিল। এবং মাসের পর মাস তা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। সেদিক থেকে তার ভাগ্য খারাপ বলতেই হবে, কারণ যার জন্য সারাজীবন সে সংগ্রাম করে গেছে তা শেষ পর্যন্ত সে দেখতে পায়নি।
আমি বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট হই কি কারণে একটা আন্দোলন এরকমভাবে ব্যর্থ হয়ে গিয়ে ধ্বংসের পথে এগিয়ে গেল। এসব অনুসন্ধানের ফলাফলে আমার দৃঢ় ধারণা হয় যে পুরনো অস্ট্রিয়াকে একত্রি করতে না পারার দরুন উভয় দলই বিরাট ভুল করেছিল।
প্যান-জার্মান দল তাদের আন্দোলনের লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য জাতিগত আদর্শ ঠিকই বেছে নিয়েছিল, সেটা হল জার্মান জাতির পুনরুত্থান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যে রাস্তাটা ওরা লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে নির্বাচিত করেছিল সেটা সঠিক হয়নি। এটা হল জাতীয়তাবাদী, কিন্তু ওরা সামাজিক সমস্যাগুলোর দিকে খুব অল্পই নজর দিয়েছিল, এবং সেই কারণেই জনতার সমর্থনও পায়নি। কিন্তু সত্যটাকে বিচার করতে গিয়ে ওরা ভুল করেছিল, যার জন্য ভুল পদ্ধতিতে ওদের একটা ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে।
খ্রিস্টান সোশ্যালিস্ট আন্দোলন অনেকগুলোর মধ্যে জার্মানদের পুনরুত্থানের ভুল ধারণা ছিল, কিন্তু ওদের বুদ্ধিমত্তা এবং দলীয় আদর্শের লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য নির্বাচিত পথটা বাছা ভাগ্যক্রমে সঠিক হয়েছিল। খ্রিস্টান সোশ্যালিস্টরা সামাজিক সমস্যাগুলোর চরিত্র ঠিকমত অনুধাবন করতে পেরেছিল; কিন্তু ইহুদীদের সঙ্গে সগ্রামের পথটা তাদের ভুল ছিল এবং তারা জাতীয়তাবাদীকে রাজনৈতিক শক্তির উৎস হিসেবে মূল্য দিতে সম্পূর্ণ ভুল করেছিল।
যদি খ্রিস্টান সোশ্যালিস্ট দল তাদের ধূর্ত বিচার বুদ্ধির সঙ্গে যা তারা জনপ্রিয় জনতা সম্পর্কে নিয়েছিল, জাতিগত সমস্যা সম্পর্কেও সেই বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করত—যেটা প্যান্-জার্মান আন্দোলনকারীরা ঠিক মত ধরতে পেরেছিল,-এবং এ পার্টি যদি সত্যিকারের জাতীয়তাবাদী হত; অথবা যদি প্যান-জার্মান আন্দোলনের নেতারা অপরদিকে ইহুদীদের এবং জাতীয়তাবাদী সম্পর্কে সঠিক ধারণার সঙ্গে খ্রিস্টান সোশ্যালিস্ট দলের মত বাস্তববাদী হত— বিশেষ করে সামাজিক দিক থেকে, তবে ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি আন্দোলন এমন রূপ নিত যা জার্মানদের গন্তব্যটাকে সফলভাবে ঘুরিয়ে দিত।
তৎকালীন দলগুলোর কারোর মধ্যে আমার মতবাদের মিল দেখতে পাইনি, আর সে কারণে তার দলভুক্ত সদস্য হবার জন্য আমার নামও লেখাইনি, এবং আমার সাহায্যের হাতও তাদের দিকে বাড়াইনি। এমনকি এসব দলগুলো তাদের সব শক্তি হারিয়ে ফেলে তখন শ্রান্ত, ক্লান্ত। তাই তাদের পক্ষে সত্যিকারের শক্তভাবে ধরে জার্মান জাতির পুনরুত্থান করাটাও সম্ভব ছিল না।
আমার অন্তরের বিতৃষ্ণা হাবুসবুর্গ শাসকদের প্রতি দিনে দিনে আরো বেশি বাড়তে থাকে।
যতই আমি এদের বৈদেশিক নীতি নিয়ে পর্যালোচনা করি, তত বেশি আমার ধারণা জন্মায় যে এ অপশাসক নিশ্চিতভাবে জার্মানদের দুর্ভাগ্যকে ডেকে আনবে। আমি দিনের পর দিন আরো বেশি উপলব্ধি করি যে জার্মান জাতির ভাগ্যের গন্তব্যস্থল কিছুতেই এদের দ্বারা নির্দিষ্ট হতে পারে না। তা একমাত্র সম্ভব কোন জার্মান সাম্রাজ্যে। এটা শুধু রাজনীতির ব্যাপারেই নয়, সংস্কৃতির ক্ষেত্রও এটা সত্যি।
এ সমস্ত ব্যাপারগুলোই সংস্কৃতি এবং শিল্পের ক্ষেত্রে আঘাত করেছে, যেখানে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে বার্ধক্য হেতু জীর্ণ বলিরেখা ফুটে উঠেছে। অথবা কমপক্ষে, যে কোন বিপদের মুখোমুখি নিয়ে গিয়ে জার্মান জাতিকে দাঁড় করাবে, অন্তত এসব ব্যাপারে। এ সত্যটা আরো বিশেষভাবে প্রকটিত স্থাপত্য বিদ্যার ব্যাপারে। আধুনিক স্থাপত্যবিদ্যা অস্ট্রিয়াতে কোন ফলাফলই দেখাতে পারেনি। কারণ রিঙ ট্রাসের বাড়িগুলো, এমনকি সমগ্র ভিয়েনার স্থাপত্যকলা জার্মান স্থাপত্যকলার তুলনায় প্রগতির দিক থেকে নেহাত ই তুচ্ছ এবং ক্রমে ক্রমে আমি এক দ্বৈত সমস্যার সম্মুখীন হই, কারণগুলো এবং বাস্তবতা আমাকে বাধ্য করে অস্ট্রিয়ার অমসৃণ শিক্ষানবীশ করতে, যদিও আমি আজ স্বীকার করি এ শিক্ষানবীশের ফলাফল শেষ পর্যন্ত ভালই হয়েছিল আমার পক্ষে। কিন্তু আমার হৃদয় পড়েছিল অন্য কোথাও।
একটা আত্মতুষ্টির মনোভাব আমার মনের ভেতরে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, এবং যত বেশি এ সরকারের অন্তঃসারশূন্যতা অনুভব করি তত বেশি আমাকে হতাশায় আচ্ছন্ন করে ফেলে। আমার দৃঢ় ধারণা হয় যে এ সরকার যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে বাধ্য। এর হাত থেকে কিছুতেই অব্যাহতি নেই। তার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে হয় এ সরকার জার্মানদের জন্য সবরকম দুর্ভাগ্যকে ডেকে আনবে।
আমার দৃঢ় ধারণা হয় এ হাবুসবুর্গ সরকার প্রতিটি জার্মানের মহানুভবতাকে বাধা দিয়ে তার গতিরোধ করবে, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি অজার্মানদের অসৎ কার্যকলাপকে সাহায্য করে যাবে। অসদৃশ্য বিভিন্ন জাতির সমষ্টি এ রাজধানীতে যেন একটা জড়বৎ পিণ্ডের মত হয়ে আছে। বিশেষ করে চিত্র-বিচিত্র চেক, স্প্যানিশ হাঙ্গেরিয়ান, রুমানিয়ান, সার্বস এবং ক্রট প্রভৃতিরা। সর্বদা এ সমাজের তলাকার বীজাণু ওখানে সব জায়গায় ছড়িয়ে থাকা ইহুদীরা আমার কাছে অত্যন্ত অপ্রীতিকর। এ বিশাল শহরটা যেন সংকর জাতীয় নীতিভ্রষ্ট অবতারদের নন্দন কানন।
জার্মান ভাষা যা আমি ছোটবেলা থেকে বলে এসেছি, তা ছিল লোয়ার ব্যাভিরিয়ার ভাষা। আমি বিশেষ ভঙ্গিতে বলার ভাষাটা কখনই ভুলতে পারিনি; আর সেই কারণেই ভিয়েনার উপভাষাও কখনো শিখিনি। যতদিন আমি সেই শহরে ছিলাম, বিদেশী পাঁচ মিশেলী পতঙ্গদের পালের প্রতি তত ঘৃণা আমার ভেতরে জেগে ওঠে। সেটা সুপ্রাচীন জার্মান সংস্কৃতির ওপরে বেতের মত নিরন্তর আঘাত করে চলে। আমার দৃঢ় ধারণা এ সরকার দীর্ঘদিন কিছুতেই স্থায়িত্ব পেতে পারে না।
অস্ট্রিয়ার তখনকার অবস্থা ছিল এক কারুকার্যময় সিমেন্টের মত, যেটা শুকিয়ে গিয়ে বহু পুরাতন এবং ভংগুর অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এ ধরনের আর্ট ছোঁয়া না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সেটা ঠিকই থাকে। কিন্তু যে মুহূর্তে বাইরের কোন আঘাত এর ওপরে এসে পড়ে সেই মুহূর্তে এটা ভেঙে হাজার হাজার টুকরো হয়ে যায়, সুতরাং এখন সবচেয়ে বড় যে প্রশ্নটা হল, কখন এ আঘাত এসে পড়বে।
আমার হৃদয় সব সময়ই স্বপ্ন দেখত জার্মান সাম্রাজ্যের। অস্ট্রিয়ার রাজতন্ত্রের সঙ্গে কখনো সঙ্গ দেয়নি। সুতরাং অস্ট্রিয়ার শাসকবর্গের অবলুপ্তি দেখে আমার মনে হয়েছিল জার্মান জাতির স্বাধীতার প্রথম ধাপ উপস্থিত।
এসব কারণগুলোই ও দেশটা ছেড়ে যাবার জন্য আমার হৃদয়ের ইচ্ছেটাকে আরো বলবতী করে তোলে; যেটা আমার যৌবনের প্রারম্ভেই কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল।
আশা করেছিলাম স্থপতি হিসেবে নিশ্চয় একদিন আমি সফল হব এবং আমার দেশের সেবায় তা বড়ভাবে বা ছোটভাবে (যা ভাগ্যের ইচ্ছা) ঢেলে দেব।
সেদেশে যারা কাজ করছিল তাদের মধ্যে আমার দীর্ঘদিন বসবাস করার কারণ হল আন্দোলনটা সেখান থেকেই শুরু হবে, যা আমার হৃদয়ে দীর্ঘদিন ধরে প্রতীক্ষা করে এসেছে, বিশেষ করে যে দেশের চৌহদ্দির ভেতরে আমাদের পিতৃভূমিতে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম সে হল জার্মান সাম্রাজ্য।
অনেকেরই হয়ত জানা নেই যে এ ধরনের ইচ্ছা কত বলবতী হতে পারে, কিন্তু আমার আবেদন দু’দল লোকের প্রতি। প্রথম দল হল এতক্ষণ পর্যন্ত আমি যা বলেছি সেই সুখগুলো যারা স্বীকার করতে নারাজ। দ্বিতীয় দল হল, যারা একবার এ সুখের স্পর্শ পেয়েছে, কিন্তু ভাগ্য নির্মম হয়ে তা কেড়ে নিয়েছে। আমি তাদের উদ্দেশ্যেই বলছি যারা তাদের মাতৃভূমিকে হারিয়েছে এবং এখনো যারা উত্তরাধিকার সূত্রে পৈতৃক সম্পত্তিটুকু বজায় রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে। তাদের মাতৃভাষা, যার ওপরে অকথ্য নির্যাতন চলছে,—তাদের জন্মভূমির প্রতি ভালবাসা এবং বিশ্বস্ত কারণে। তারা বুকের ভেতরে প্রবল ইচ্ছা নিয়ে অপেক্ষা করছে, কখন পিতৃভূমির উষ্ণ ক্রোড়ে ফিরে যেতে পারবে। তাদের উদ্দেশ্যে আমার এ বক্তব্য, এবং আমি জানি তারা আমার বক্তব্যকে সম্যভাবে অনুধাবন করতে পারবে।
যে তার পিতৃভূমি থেকে বিতাড়িত—সে-ই উপলব্ধি করতে পারবে কী গভীর সেই স্বদেশের প্রতি আকুলতা যা তাকে নির্বাসিত ভাবতে বাধ্য করেছে। এটা হল একটা চিরস্থায়ী মনস্তাপ যার কোন প্রকার সান্ত্বনা নেই যতক্ষণ পর্যন্ত না পিতৃঘরের দরজা খোলা যায়। একমাত্র তখনই শিরা উপশিরায় প্রবাহিত চঞ্চল রক্ত শান্তি পেতে পারে তাদের নিজভূমিতে আশ্রয় পেয়ে।
ভিয়েনা আমার পক্ষে কঠিন বিদ্যালয় ছিল; কিন্তু এটাই আমাকে জীবনে সুগভীর শিক্ষাও দিয়েছিল। আমাকে তখন বড়জোর বালক বলা চলে যখন আমি সে শহরে আসি, এবং যখন আমি সে শহর ছাড়ি তখন আমি মনের দুঃখে ভারাক্রান্ত বিষন্ন যুবক। ভিয়েনাতেই আমার আন্তর্জাতিকতাবাদের দীক্ষা এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিশ্লেষণের শুরুও হয় এ শহরেই। সেই দিনকার সেই আন্তর্জাতিকতাবাদ চিন্তাধারা, রাজনৈতিক মতবাদ আমাকে আর কখনই ছেড়ে যায়নি। যদিও তারা ভবিষ্যতে ভিন্নমুখী হয়ে বিভিন্ন পথে ছুটেছে। বর্তমানে আমি আমার সেই ফেলে আসা শিক্ষানবীশ দিনগুলোর সঠিক মূল্যায়ণ করতে পারি।
এ কারণেই আমি সেদিনগুলোর বর্ণনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দিয়েছি। এ ভিয়েনাই আমাকে রূঢ় বাস্তব শিক্ষা ও সত্যের সন্ধান দেয়, যা ভবিষ্যতে আমার রাজনৈতিক আদর্শের পটভূমি হিসেবে কাজ করে পরবর্তী পাঁচ বছর ধরে জনতার সমর্থন লাভ করে। আমার ইহুদী, সামাজিক গণতন্ত্র বিশেষ করে মার্কসবাদ সম্পর্কে কোন ধ্যান ধারণাই ছিল না। এবং সেদিন তাই অত পরিশ্রম এবং পড়াশোনায় ভাগ্যের লাঞ্ছনায় তৈরি করেছিলাম নিজেকে।
পিতৃভূমির দুর্ভাগ্যের জন্য যে হাজার হাজার লোক মনে মনে নিজেদের তোলপাড় করে চলেছে, তাদের পক্ষেও একজন যে প্রবল বাঁচার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজের ভাগ্যকে তৈরি করেছে, তার মত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা সম্ভব নয়।
——–
*হেরোডটি তার লেখায় গ্রীক বিশ্বাসঘাতক এ্যফিলটেসের বর্ণনা করেছেন। থার্মোপাইলের যুদ্ধে প্রায় পরাজিত পারস্যরাজ জেরেসের কাছে গিয়ে ফিলটেস্ প্রস্তাব করে যে তাকে যদি মূল্য দেওয়া হয়, তবে সে গ্রীক দেশে ঢোকার গুপ্তপথ দেখিয়ে দেবে। প্রাপ্তিযোগের পর পাহাড়ের গিরিপথ দিয়ে একদল পারস্যদেশীয় সৈন্যকে জেনারেল হাইডেরলেসের অধীনে পথ দেখিয়ে দেয়। কিন্তু গ্রীক সৈন্যরা, স্পার্টার রাজা লিওনিডাসের নেতৃত্বে দু’মুখী পারস্য অভিযানের মোকাবিলা সেই সংকীর্ণ গিরিপথে করে। সেই সংগ্রামে লিওনিডাসের। মৃত্যু হয়।
০৪. মিউনিক
অবশেষে আমি এলাম মিউনিকে, সেটা ১৯১২ সালের বসন্তকাল। শহরটা আমার পূর্বপরিচিত; কারণ এ শহরের চার দেওয়ালের গণ্ডির মধ্যে আমার বেশ কয়েকটা বছর কেটেছে। এর কারণ হল আমার স্থাপত্যবিদ্যায় পড়াশুনার জন্য জার্মান প্রধান শহরগুলো শিল্পের কেন্দ্র হওয়াতে আমার দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল মিউনিকের দিকে। জার্মানিকে চিনতে গেলে মিউনিক না দেখলে জার্মান শিল্পকলা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ করাও সম্ভব নয়।
এসব জিনিস বিচার করলে দেখা যাবে, যুদ্ধ-পূর্ব জীবনটা আমার অনেক সুখের ছিল। যদিও আমার রোজগার অত্যন্ত অল্প ছিল, তবু শুধু ছবি আঁকার জন্য আমি জীবন ধারণ করিনি। আমি ছবি এঁকেছি প্রাণ ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তাই যোগাতে আর পড়াশুনা করার নিমিত্তে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল আমার নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আমি নিশ্চয়ই পৌঁছাব এবং এ বিশ্বাসই আমার দৈনন্দিন ছোট ছোট দুঃখগুলোকে পেরিয়ে নিয়ে যেতে যথেষ্ট ছিল; যার জন্য আমি কখনই উদ্বিগ্ন বোধ করিনি।
উপরন্তু আমার প্রবাসের প্রথম মুহূর্ত থেকেই এ শহরটাকে ভালবেসে ফেলেছিলাম, যা আমি আর অন্য কোন জায়গার প্রতি-ই উপলব্ধি করিনি। এ হল জার্মান শহর! নিজের মনেই আমি বারবার উচ্চারণ করতাম। ভিয়েনার থেকে কত আলাদা। আরেকটা আনন্দের বিষয় হল এখানে লোকে জার্মান ভাষায় কথা বলে, যেটা ভিয়েনার অন্য ভাষার চেয়ে আমার নিজের বলার ভাষায় অনেক কাছাকাছি। মিউনিকের বাক পদ্ধতি আমার ছেলেবেলার কথা স্মরণ করিয়ে দিত, বিশেষ করে যারা লোয়ার ব্যাভেরিয়া থেকে মিউনিকে আসত। হাজার বা তারও বেশি জিনিস ছিল যা আমি অন্তর থেকে ভালবাসতাম; অথবা মিউনিকে থাকাকালে যাদের প্রতি ভালবাসার জন্য আকৃষ্ট হয়েছিলাম। কিন্তু যা আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছিল, তাহল শহরের শিল্পপ্রেরণার সঙ্গে গ্রামের মাটির কলা চাতুর্যের বন্ধন, যার সুন্দর ছন্দ হোব্রা হাউস থেকে ওডেন পর্যন্ত, অক্টোবর উৎসব থেকে পিনাকোনোক পর্যন্ত বিস্তৃত। মিউনিকের মত আর কোন জায়গা আমার হৃদয়ের সুতোয় এত জড়ানো নয়; কারণ আমার ব্যবহারিক জীবনের উন্নতির সঙ্গে এ মিউনিক শহর ওতপ্রোতভাবে জড়ানো এবং সত্যি বলতে কি, এ শহরটা দর্শনের পর থেকেই আমার অন্তরে খুশির বান ডাকে, বিশেষ করে এ সুন্দর শহর আমার আত্মতৃপ্তিও এনে দেয়। আমার মনে হয় যাদের ভেতরে সৌন্দর্যবোধের আশীর্বাদ ঈশ্বর দিয়েছেন, বাণিজ্যিক শিল্পকলা ব্যতিরেকে তারাই এ শহরকে ভাল না বেসে থাকতে পারবে না।
আমার পেশাগত কাজ ছাড়াও বর্তমান রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে আমি যথেষ্ট পড়াশুনা করতাম। বিশেষ করে বৈদেশিক সম্পর্কিত বিষয়গুলোই আমাকে বেশি করে আকৃষ্ট করত। আমি পুরো ব্যাপারটাই জার্মান নীতি কুটুম্বিতার দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করতাম, যদিও ভিয়েনা শহরে দিনগুলো কাটানোর পর আমার ধারণা হয়েছিল, সমস্ত ব্যাপারটাই ভুলে ভর্তি। কিন্তু ভিয়েনাতে থাকাকালীন আমি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারিনি ঠিক জার্মান সাম্রাজ্য কত আত্মভ্রমের পথে এগিয়ে গেছে। ভিয়েনার দিনগুলোতে আমার এ ধারণা হয়েছিল যা বলা যেতে পারে, আমি নিজেকে বুঝিয়েছিলাম যাতে জার্মানদের ভুলগুলো হাল্কাভাবে নিতে পারি বা কম নজরে আসে। হয়ত বা জার্মানের শাসকবর্গের জানা ছিল বাস্তবে এ ধরনের সম্পর্কের মূল্য কতটুকু। কিন্তু কোন একটা রহস্যজনক কারণে তারা জনসাধারণের কাছ থেকে পুরো ব্যাপারটা গোপন করে গেছে। তাদের ধারণা ছিল বিসমার্কের মাধ্যমে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে, তাকে তাদের সমর্থন জানিয়ে যাওয়া উচিত। হঠাৎ কিছু করে বসার ফলাফল ভাল দাঁড়াবে না; এছাড়া অন্য কোন কারণ সম্ভবত নেই যার জন্য বিদেশী রাষ্ট্রগুলো এ দেশের ভেতরের সঙ্কীর্ণমনা লোকগুলোর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল।
কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে আমার যোগাযোগের ফলে, ভয়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলাম যে আমার চিন্তাধারা ভুল ছিল। সবচেয়ে অবাক লাগল দেখে যে যারা প্রায় সব বিষয়েই ভালরকম খবরাখবর রাখে, তাদের পর্যন্ত হাবুবুর্গ রাজতন্ত্র সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। সাধারণ জনসাধারণের ভেতরে বাঁধাধরা একটা ধারণা ছিল যে অস্ট্রিয়া গণনার মধ্যে ধরার মত শক্তিশালী এবং তারা বিপদের সময় পেছনে এসে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। সাধারণ মানুষ তখন পর্যন্ত অস্ট্রিয়াকে জার্মান রাষ্ট্র বলেই বিবেচনা করে এসেছে, এবং ভেবে এসেছে যে ওদের ওপর সত্যিই নির্ভর করা যায়। জার্মানির মতই লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ দিয়ে ওদের শক্তির পরিমাপ করা ছিল। প্রথমত, তারা ভাবতে পারেনি যে অস্ট্রিয়া কোন জার্মান সাম্রাজ্যই নয়, দ্বিতীয়ত অস্ট্রিয়ার বর্তমান অবস্থা তাকে দুঃসাহসে ভর করে ধ্বংসের একেবারে মুখে ঠেলে এনে ফেলেছে।
সে সময়ে অস্ট্রিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্পর্কে আমার জ্ঞান যে কোন পেশাদারী কুটনীতিজ্ঞদের চেয়ে বেশি ছিল। বদ্ধচক্ষুবশত দেখতে অক্ষম এসব কুটনীতিজ্ঞদের দল হোঁচট খেতে খেতে ধ্বংসের দিকে চলে। সরকারি অফিসগুলো থেকে যে প্রচলিত মতবাদে তাদের কর্ণপটহ বিদীর্ণ করা হয়েছে, সাধারণ মানুষের মধ্যে সেই মতবাদেরই প্রতিধ্বনি শোনা যেত।
এবং এ সরকারি অফিসারের দল এ কুটুম্বিতার কাছে হাটু গেড়ে এমন ভাব করত যেন তারা সোনার বাছুরের কাছে নতজানু হয়েছে। তারা বোধহয় ভাবত যে তাদের বিনয় এবং অমায়িকতায় অন্য পক্ষের সততার অভাব ঢাকা পড়ে যাবে। এভাবে তারা প্রতিটি নির্দেশের পুর্ণ মর্যাদা দিত।
এমন কি ভিয়েনাতে থাকাকালীন মাঝে মাঝে সরকারি অফিসারদের ভাষ্য এবং ভিয়েনার সংবাদপত্রের বিষয়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য দেখে রেগে যেতাম। কিন্তু তবু ভিয়েনা ছিল জার্মান শহর; অন্তত দূর থেকে দেখতে তো বটেই। তাই ভিয়েনা ছেড়ে বেরোলেই সবাইকে অন্য ধরনের অবস্থার মুখোমুখি হতে হত। বিশেষ করে শ্লাভ কোন দেশে গেলে। প্রাগের সংবাদপত্রগুলোর প্রতি নজর দিলে এক লহমায় বোঝা যেত এ তিন কুটুম্বের বাজীকরের ভেল্কী কত উন্নত। প্ৰাগে অবশ্য সেই সুদক্ষ রাজনীতির ভাগ্যে গালাগাল আর ঘৃণা মিশ্রিত নাক সিটকানো ছাড়া আর কিছু জোটেনি। এমন কি শান্তির সময় বিজয় উৎসবে যখন দুই সম্রাট পরস্পরের কপালে চুম্বন করে বন্ধুত্বের চিহ্ন স্বরূপ, সেইসব সংবাদপত্রগুলো তখনো বিশ্বাস করতে রাজী নয় যে–মুহূর্তে হঠাৎ ঝিকমিক করে জ্বলে ওঠা গৌরব নিবালির্দেনের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করতে গেলে তা নিভে যাবে।
কয়েকবছর পর প্রচণ্ড ক্রোধ জেগে ওঠে; এ মৈত্রী বাস্তবের পাথরে পরীক্ষার জন্য টেনে আনা হয়। ইতালি যে ত্রি-পাক্ষিক মৈত্রীর জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে যায় শুধু তাই নয়, অপর দুজনকে একা ফেলে রেখে সে গিয়ে শত্রুশিবিরেও যোগ দেয়। ইতালি অস্ট্রিয়ার সঙ্গে দাঁড়িয়ে এক সারিতে যুদ্ধ করেছে, — এ কথা অবিশ্বাস্য। অবশ্য কুটনীতজ্ঞদের মত যদি সে অন্ধত্বরোগে না ভোগে। ঠিক এ ধারণাটা অস্ট্রিয়ার লোকদের তখন ছিল।
অস্ট্রিয়াতে একমাত্র হাবুবুর্গ আর অস্ট্রিয়ার জার্মানরা এ মৈত্রী সমর্থন করেছিল। হাবুসবুর্গ অত্যন্ত ধুর্তামীর সঙ্গে আঁক কষে এবং নিজেদের স্বার্থে ও প্রয়োজনে এ কাজ করেছিল। জার্মানরা সরল বিশ্বাস এবং রাজনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ থাকায় এ মৈত্রীকে সমর্থন জানিয়েছিল। তাদের এ সরল বিশ্বাস ছিল যে এ ত্রি-পাক্ষিক মৈত্রীকে সমর্থন জানিয়ে তারা জার্মান সাম্রাজ্যের সেবা করছে এবং তাদের প্রতিরক্ষাকে শক্ত ও একত্রিত করায় সাহায্য করছে। তবু বলতে বাধা নেই, এ ধরনের ধ্যান ধারণার জন্য তাদের রাজনৈতিক অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। আসলে এ ধারণার বশবর্তী হয়ে কাজ করায় তা জার্মান সাম্রাজ্যের সাহায্যের বদলে, আসলে একটা মৃতকল্প রাষ্ট্রের সঙ্গে শৃঙ্খল দিয়ে বাঁধা হয়েছে–যার যে কোন মুহূর্তে কবরের সঙ্গে গাটছাড়া বাঁধার সম্ভাবনা ছিল। সর্বোপরি, এ রাস্তায় হাবুবুর্গ নীতি অস্ট্রিয়াকে জার্মান শূন্য করতে সাহায্যই করেছে।
এ মৈত্রীর জন্য হাবুসবুর্গের বিশ্বাস ছিল যে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে জার্মান সম্রাট নাক গলাবে না। সুতরাং তারা এ জার্মান শূন্য করার কাজটা সহজেই কোনরকম দায়সারা ভাবে করে যেতে পারবে। তাদের আভ্যন্তরীণ নীতি ছিল ধীরে ধীরে অস্ট্রিয়াকে জার্মান শূন্য করা। শুধু জার্মান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিই নয়, কোনদিক থেকেই প্রতিবাদ আসার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু একজনের পক্ষে এ জার্মান অস্ট্রিয়ার মৈত্রী কখনই ভোলা সম্ভব হয়নি এবং সেই কারণেই তাদের স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তারা তিরস্কারের যোগ্য এ কারণে যে এ নীতির মাধ্যমে তারা এ দ্বৈত রাজতন্ত্রের ভেতরে শ্লাভ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় রত।
অস্ট্রিয়ায় বসবাসকারী জার্মানরা কি করতে পারে, যখন জার্মান সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা প্রকাশ্যেই তাদের বিশ্বাস এবং আস্থা হাবুবুর্গ শাসকের কাছে জানিয়ে দিয়েছেতাদের কে এতে বাধা দেবে? তবে তো প্রকাশ্যেই সবাই বলে বেড়াবে যে এরা এদের জ্ঞাতিবর্গের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে নিজেদের জাতীয় স্বার্থে, তারা যারা এত যুগ ধরে এত ত্যাগ স্বীকার করে এসেছে।
একবার যদি কোনক্রমে অস্ট্রিয়ার ওপর থেকে জার্মান প্রভাব মুছে ফেলা যায়, তবে আর এ মৈত্রীর মূল্য কতটুকু! যদি এ ত্রি-পাক্ষিক মৈত্রী জার্মানদের পক্ষে লাভজনক হত তবে উচিত ছিল না অস্ট্রিয়াতে জার্মানদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখা? অথবা, কারোর পক্ষে কি বিশ্বাস করা সম্ভব যে জার্মানি হাবুসবুর্গ সাম্রাজ্যের মৈত্রী সংঘে টিকে থাকতে পারে যার নেতৃত্ব শ্লাভদের অধিকারে?
জার্মান কুটনীতিজ্ঞদের সরকারি ধ্যান ধারণা এবং সাধারণ জনতার হাবুবুর্গের আভ্যন্তরীণ সম্পর্কে চিন্তাধারা শুধু বোকামীরই পরিচায়ক নয়, সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞও বটে। এ মৈত্রীকে শক্ত পটভূমি ধরে নিয়ে তারা সত্তর লক্ষ একটা জাতির ভবিষ্যত নিরাপত্তা এবং অস্তিত্ব তাদের হাতে সঁপে দিয়েছে, কিন্তু সেই সঙ্গে তার অংশীদারকে সেই শক্ত পটভূমি ভাঙার ক্ষমতা দিয়েছে, যা সে যথারীতি এবং স্থির সংকল্পে করে চলেছে। এমন একদিন আসবে যখন ভিয়েনার রাজনীতিজ্ঞদের সঙ্গে কাগজে সই করা চুক্তি ছাড়া আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। শেষপর্যন্ত জার্মানির কাছে এ মৈত্রীটাই হারিয়ে যাবে। ইতালি অবশ্য একাজ আগেই আরম্ভ করে দিয়েছিল।
যদি জার্মানির লোকেরা ইতিহাস পড়ত এবং কিছুটা মনস্তত্ত্বও বুঝতে পারত তবে কখনই মুহূর্তের জন্য বিশ্বাস করত না যে ভিয়েনা রাজদুর্গ একত্রে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে। সম্পূর্ণ ইতালি আগ্নেয়গিরির মত জ্বলে উঠত যদি একজন ইতালিয়ানকেও হাবুসবুর্গ যুদ্ধের জন্য পাঠানো হত।
এদের প্রতি ইতালিয়ানদের ঘৃণা এতই তীব্র ছিল যে ইতালিয়ানরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে এদের শক্র ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারত না। একাধিকবার আমি এ ঘটনার সাক্ষী যখন, তখন ইতালিয়ানদের এ মৈত্রীর বিরুদ্ধে ক্রোধে ফেটে পড়তে দেখেছি। হাবুসবুর্গ রাজতন্ত্র অনেক শতাব্দী ধরে ইতালির মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার বিরুদ্ধে যে অপরাধ করেছে তা ভোলা অসম্ভব; এমন কি প্রচণ্ড সদিচ্ছা থাকলেও। কিন্তু এ সদিচ্ছা কারোর ভেতরেই ছিল না; না জনসাধারণ — না সরকার। সুতরাং ইতালির সামনে ছিল দু’টো পথ খোলা–মৈত্রী অথবা যুদ্ধ। প্রথমটাকে বেছে নেওয়ার সুবিধে হল ধীরে ধীরে দ্বিতীয়টার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার সুযোগ।
বিশেষ করে অস্ট্রিয়া এবং রাশিয়ার সম্পর্কটা যখন যুদ্ধের মাধ্যমে নিষ্পত্তির দিকে এগোচ্ছিল, তার মৈত্রী সম্বন্ধে জার্মান নীতি শুধু অর্থহীন-ই নয়, বিপজ্জনকও বটে। এটাই হল কোন উদার অথবা যুক্তিপূর্ণ চিন্তাধারার অভাবের উজ্জ্বল উদাহরণ।
কিন্তু তাহলে এ মৈত্রীর কারণটা কি? জার্মান রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য এ মৈত্রীর চেয়ে নিজেদের উৎসের ওপর নির্ভর করা উচিত ছিল। কিন্তু জার্মান রাষ্ট্রের জার্মানদের ভবিষ্যত নিরাপত্তার প্রশ্নটাই তুলে ধরে বেশি করে।
তাহলে বাকি যে প্রশ্ন রইল, তা হল এরকম : নিকট ভবিষ্যতে জাতির স্বরূপটা কি হবে? বলা যেতে পারে, সময়টা এমন হওয়া উচিত যাতে পূর্বাভাস করা যায়। এবং কিভাবে ইউরোপের জাতিদের মধ্যে শক্তির বণ্টন হওয়া উচিত যাতে জাতির সার্বিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা সম্ভব?
জার্মানির বিদেশ নীতি যে রাজনীতিবিদ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তার পরিষ্কার বিশ্লেষণ করলে নিচের ধারণায় পৌঁছানো যায়?
জার্মানির লোক উৎপাদন তখন বছরে প্রায় ন’লক্ষ। এ বিরাট কলেবর নতুন আসা নাগরিকদের প্রয়োজনীয় সবকিছু দেওয়ার অক্ষমতা শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের ওপর বিপর্যয়কারী ঘটনা হিসেবে নেমে আসবে, যদি না এ বিষয়ে পূর্বে কোন ব্যবস্থা নির্ধারণ করা যায়। তবে নিশ্চিত যে তাদের ওপর দুঃখ এবং অনাহার নেমে আসবে। এ বিভৎস বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার চারটে পথ আছে।
প্রথমত এ ব্যাপারে ফরাসী উদাহরণ গ্রহণ করে কৃত্রিম উপায়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে এ বিশাল জনতার উপস্থিতি বন্ধ করা সম্ভব।
কয়েকটি অবস্থায় বিপদের মুখে অথবা প্রাকৃতিক দৈবদুর্যোগে বা মাটি যদি পর্যাপ্ত ফসল না দেয় তবে প্রকৃতি এভাবে কোন কোন দেশে এবং জাতের মধ্যে নিজে থেকেই জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। কিন্তু পদ্ধতিটি যথেষ্ট পরিমাণেই নিষ্ঠুর। তবে এতে জননক্ষমের কার্যক্ষমতাকে বাধা দেওয়া হয় না; কিন্তু যারা অতো শক্তিশালী অথবা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নয় এভাবে তাদের বংশাবলী অস্তিত্ব হারিয়ে কোন এক অজানাকে আলিঙ্গনে বাঁধে। যারা এ অস্তিত্বরক্ষার কঠিন পথ বেয়ে বেঁচে থাকে তাদের ইতিমধ্যেই সহস্রগুণ পরীক্ষা হয়ে গেছে যে তারা যে কোন অবস্থাতেই বেঁচে থাকতে পারে এবং জননক্ষম। সুতরাং ব্যাপারটার তো পুনরাবৃত্তি হয়েই চলেছে। এভাবে নির্দয়তার সঙ্গে ব্যক্তির লড়াই যে মুহূর্তে সে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে অক্ষম হবে, তাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। প্রকৃতিই জাতির শক্তি বজায় রাখে এবং উন্নততর শ্রেণীর অন্তর্গত শ্রেণী উৎপাদন করে এবং তাকে বাড়িয়ে নিয়ে চলে।
সংখ্যার অবরোহণ কিন্তু শক্তির উচ্চতাই ডেকে আনে। অবশ্যই একক ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য। এবং শেষে পুরো প্রজাতিটাকেই বলশালী করে তোলে।
মানুষ প্রকৃতির বন জঙ্গলের খণ্ড খণ্ড অংশ নয়। সে মনুষ্যত্ব নামক মাল মশলার তৈরি তার জ্ঞান নির্দয়া জ্ঞানের রাণীর চেয়ে অনেক বেশি। সে একক ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব রক্ষায় বাধা দেয় না। কিন্তু জননক্রিয়ায় বিরত থাকতে পারে। একক ব্যক্তিত্বের কাছে, যে শুধু নিজের কথাই ভাবে, সমস্ত জাতির কথা নয়; এ ধরনের চিন্তাধারা তার কাছে অনেক বেশি মনুষ্যত্ববোধ সম্পন্ন বলে মনে হবে এবং অপরটায় মনুষ্যত্ব ব্যাপারটাকেই সে খুঁজে পাবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ব্যাপারটার পরিণতি সম্পূর্ণরূপে উল্টো।
এ জননক্রিয়া বন্ধ না করে এবং একক ব্যক্তিত্বকে প্রস্তুত থাকার সংগ্রামে তৈরি করে নিতে পারলে, প্রকৃতি তার মধ্যে থেকে শ্রেষ্ঠ মানুষটাকে বেছে নেবে এবং উন্নত একটা প্রজাতিএ পদ্ধতির মাধ্যমে তৈরি হবে স্বাভাবিক উপায়ে। কিন্তু মানুষ নিজে থেকেই এ জননক্রিয়া সীমাবদ্ধ রাখে এবং জেদী হয়ে যে এসেছে তাকে যে কোন মূল্যে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে। ইশ্বরের ইচ্ছাকে শুদ্ধিকরণ মনে হয় এবং যেন অনেক বেশি জ্ঞানের পরিচায়ক এবং মনুষ্যত্ববোধ সম্পন্ন। প্রকৃতির ওপর জিততে পেরে সে আনন্দে উফুল্ল হয় এবং এভাবে দেখা যায় প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতেও পারা যায়। সেই সর্বশক্তিমান পিতার প্রিয় বানরটি এ ভেবে খুশি হয় যে সেই সংখ্যাবিষয়ক সীমাবদ্ধতায় সে কিছুটা আলোড়ন আনতে পেরেছে। কিন্তু তাকে যদি বলা যায় যে পদ্ধতিটি ব্যক্তিত্বের গুণ অধোগতি করে দেয়, তবে সে নিশ্চয়ই সুখী হবে না।
যে মুহূর্তে এ জননক্ষম কার্যক্ষমতাকে বাধা দেওয়া হয়, জন্মের সংখ্যাও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে; অস্তিত্বরক্ষার জন্য স্বাভাবিক সংগ্রাম, যা শুধু স্বাস্থ্যবান এবং শক্তিশালী ব্যক্তিকেই বাঁচিয়ে রাখে, তার বদলে ক্ষীণ, দুর্বল এবং রুগ্নদের পর্যন্ত যে কোন মূল্যে বাঁচিয়ে রাখার প্রতিযোগিতায় মানুষ উন্মত্ত হয়ে পড়ে।
কিন্তু এ নীতি যদি চালিয়ে যেতে দেওয়া যায় তার শেষ ফলাফল হবে জাতি তার অস্তিত্বটাই হয়ত বা পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলবে। যদিও মানুষ কিছুদিনের জন্য জননক্রিয়ার চিরসত্য আইনটাকে উপেক্ষা করতে পারে, কিন্তু সত্বর অথবা কিছু পরে প্রতিহিংসা ঠিকই মাথা উঁচু করবে। একটি শক্তিশালী জাতি দুর্বল হয়ে পড়ে সমস্ত জাতিকে উচ্ছেদের পথ টেনে নিয়ে যাবে। শেষে চাপা পড়া আকুতি ধীরে ধীরে একসময় রূপ নিয়ে একক ব্যক্তিত্বের তথাকথিত মনুষ্যত্ববোধটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলে প্রকৃতি তার স্বাভাবিক কাজ করে যাবে, যা সবলকে স্থান করে দেবার জন্য দুর্বলকে মুছে ফেলবে।
যে কোন নীতি যা জন্ম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জাতির অস্তিত্ব রক্ষায় সচেষ্ট, তা কিন্তু সেই জাতির ভবিষ্যৎ হরণ করে।
দ্বিতীয় সমাধান হল অন্ত উপনিবেশনে। এ কথাটা নিয়ে আমাদের সময়ে অনেক নাড়াচাড়া হয়েছে এবং প্রায় প্রত্যেকেরই হৃদয় ভরে উঠেছে ব্যাপারটায়। এ উপদেশের অর্থটা খুব ভাল। তবে অনেকেই এটা ভুল বুঝেছে।
এটা অতি সত্যি যে জমির উৎপাদন ক্ষমতা একটা সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে বাড়নো যেতে পারে, সেই জমির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে জার্মানির ক্রমবর্ধমান জন্মের একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুরাহাও করা চলতে পারে, যাতে অনাহারটা এড়ানো যায়। কিন্তু আমাদের বোঝা উচিত যে জন্মের থেকেও জীবন-যাপনের মান অনেক বেশি দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। খাদ্য এবং পোশাকের চাহিদা বছরে বছরে অনেক বেশি বেড়ে চলেছে। এবং সেই চাহিদার পরিমাপের সঙ্গে আমাদের প্রপিতামহদের সময়কার চাহিদার কোন তুলনাই হয় না। অন্ততপক্ষে শ’খানেক বছর আগেকার ব্যাপার ধরলে। সুতরাং এ ধারণাটা সম্পূর্ণ ভুল যে জমির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াতে পারলেই ক্রমবর্ধমান জনতার খাদ্যের চাহিদা মেটানো সম্ভব। না। সেটা কিছুদূর পর্যন্ত সম্ভব। জমি যে পরিমাণে বেশি উৎপাদন করবে, তার একটা ভাগ তো দিনে দিনে যে চাহিদা বেড়ে চলেছে তাদেরই দাবি মেটাতে চলে যাবে। এমন কি যদি এ চাহিদা সবচেয়ে নিচু রেখায় টেনে সীমাবদ্ধ রাখা যায়, এবং আমরা যদি আমাদের সমস্ত শক্তি নিবিড় চাষে নিয়োজিত করি, তবু আমরা এমন একটা সীমায় এসে থমকে দাঁড়াব, যা প্রকৃতির সহজাত স্বাভাবিক ক্ষমতা। আমরা কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য যত পরিশ্রমই করি না কেন, তবু আমরা মাটির উৎপাদন ক্ষমতার সীমার বাইরে কি করে যাব। সুতরাং দেখা যাচ্ছে সেই ধ্বংসের সময়টা আমরা কিছু সময়ের জন্য পিছিয়ে দিতে পারলেও শেষপর্যন্ত তা একদিন এসে হাজির হবেই। প্রথমে মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে, ঠিক খারাপ শস্য উৎপাদনের পরেই ইত্যাদি। দিনে দিনে যত লোক বেড়ে চলবে, দুর্ভিক্ষও ঘন ঘন হবে–দুই দুর্ভিক্ষের মধ্যবর্তী সময়টা কমে গিয়ে। শেষে একমাত্র প্রচুর ফসল উৎপাদনের সময় ছাড়া–দুর্ভিক্ষ হবে নিত্যদিনের সঙ্গী।
অবশেষে এমন একসময় আসবে, যখন প্রচুর ফসলের বছরগুলোতেও আর কুলানো যাবে না। সুতরাং ক্ষুধা আবার জাতির দরজায় এসে আঘাত করবে। প্রকৃতি আবার পা ফেলে এগিয়ে আসবে এবং কারা বাচার যোগ্য তা বাছতে শুরু করবে। অথবা, মানুষ যদি তার নিজের সংখ্যাধিক্য না বাড়াবার জন্য কৃত্রিম উপায়ে গ্রহণ করে, তার জন্য কী ভীষণ ফলাফলের মুখোমুখি তাকে তার জাতি বা প্রজাতির জন্য হতে হবে তা আমি আগেই বলেছি।
এখানে হয়ত বা কেউ আপত্তি জানিয়ে বলবে, মানুষ্যত্ববোধের জন্যই ভবিষ্যত, এবং একক কোন জাতি বা ব্যক্তির পক্ষে এখনই তা এড়ানো সম্ভব নয়।
প্রথম নজরে মনে হবে, এ আপত্তির পেছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে; কিন্তু আমাদের নিচের ব্যাপারগুলোকেও গণনার মধ্যে আনা উচিত।
নিশ্চয়ই সেদিন আসবে, যখন সমস্ত মানব জাতিকেই তার প্রজাতিদের বৃদ্ধি বন্ধ রাখতে হবে। কারণ তখন আর সম্ভব হবে না জমির উৎপাদনের সঙ্গে তাল রেখে এ নিত্য বর্ধিত জনসংখ্যাকে পোষণ করার। প্রকৃতিকে তখন তার পদ্ধতি কাজে লাগাতে দিতে হবে। অথবা মানুষ সেই সীমাবদ্ধতার কাজ নিজে হাতেই তুলে নেবে। এবং আজকে যা প্রচলিত তার থেকে উন্নত কোন ভারসাম্য সম্পন্ন পথ খুঁজে বার করতে হবে। কিন্তু তখন সমস্যাটা হয়ে দাঁড়াবে সমস্ত মনুষ্যজাতির; আজ যেখানে আরো বেশি জমি দখল করার জন্য প্রচুর শক্তি এবং বীর্য নেই বলে যে সমস্ত জাতিকে কষ্ট পেতে হচ্ছে যাতে তাদের প্রয়োজন মেটে, আজকের যা অবস্থা, সারা পৃথিবীতে বহু অনাবাদী জমি পতিত পড়ে আছে, সেই জমিগুলো শুধু কর্ষণের অপেক্ষা। এবং এটা ধ্রুব সত্যি যে প্রকৃতি সেই জমিগুলো কোন জাতি বা প্রজাতির জন্য পশুচারণের ক্ষেত্র ভেবে ফেলে রেখে দেবে না। এগুলো ভবিষ্যতের জন্য প্রকৃতিরই সঞ্চয় করে রাখা ভাণ্ডার। এ জমিগুলো তাদের জন্য অপেক্ষা করছে, যারা নিজেদের শক্তিতে সেগুলো দখল করে পরিশ্রমের দ্বারা সেগুলো আবাদী জমিতে পরিণত করবে।
রাজনৈতিক সীমান্ত বলতে প্রকৃতি কিছু বোঝে না। পৃথিবীতে প্রাণ সঞ্চার করে দিয়ে তার কাজ হচ্ছে শক্তির লড়াই চুপ করে দেখা। যারা শক্তিমান, সাহসী এবং পরিশ্রমী তাদের সে বুকের কাছে টেনে নেয়। এবং তারা তার রাজ্যে বাঁচার একছত্র সম্রাট।
যদি একটা জাতি নিজেদের উপনিবেশে আবদ্ধ রাখে, অপরদিকে অন্য জাতিরা তাদের জমির সীমারেখা নিত্য বাড়িয়ে চলেছে, পৃথিবীতে সেই জাতি তখন বাধ্য হয় জন্ম নিয়ন্ত্রণের পথ বেছে নিতে, যখন অন্য জাতিরা তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে, এ অবস্থা শেষমেষ এসে দাঁড়াবেই। যদি জাতিটার দখলে জমির পরিমাণ কম হয়, তবে অবস্থাটা সত্বর এ পর্যায়ে এসে উপস্থিত হবে; বর্তমানে এটা দুর্ভাগ্যজনক যে শ্রেষ্ঠ জাতিসমূহ–অথবা, খুব স্পষ্ট করে বলতে গেলে একমাত্র সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতিরাই মানব জাতির প্রগতির ধ্বজার একমাত্র বাহক,–তারা অন্ধভাবে যুদ্ধ বর্জন বাঞ্চনীয় এবং সম্ভব এ মতবাদ মেনে নিয়েছে; এভাবে তারা আর নতুন জমিও দখল করছে না। শুধু নিজেদের উপনিবেশটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট হয়ে রয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অনেক নিচু গুণসম্পন্ন জাতিরা উপনিবেশের জন্য পৃথিবীর অনেক জায়গা দখল করে রেখেছে; অবস্থাটা শেষ পর্যন্ত কোথায় এসে দাঁড়াবে নিচে তার ফলাফল দেওয়া হল :
যে সব জাতি সাংস্কৃতিক ব্যাপারে অন্য জাতের চেয়ে উঁচু, কিন্তু কম নির্দয়, তারা তাদের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি রাখতে বাধা হবে; কারণ তাদের সীমাবদ্ধ জমির আয়তনের জন্য–যার দ্বারা এর বেশি লোকসংখ্যাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়; কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতিরা তাদের লোকসংখ্যা বাড়িয়েই চলতে পারে, কারণ তাদের কাছে তো প্রচুর জমি পড়ে রয়েছে। অন্য কথায়, এ ব্যাপার যদি দীর্ঘদিন ধরে চলতে দেওয়া হয়, এক সময় সমস্ত পৃথিবীটারই দখল নিয়ে বসবে এ অপেক্ষাকৃত কম সংস্কৃতিসম্পন্ন জাতিরা, যাদের শক্তি এবং কাজ করে চলার ক্ষমতা বর্তমান।
এমন এক সময় আসবে, সুদূর ভবিষ্যতে হলেও, যখন বিকল্প হিসেবে মাত্র দুটো পথ খোলা থাকবে : হয় পৃথিবীটা শাসিত হবে আমাদের আধুনিক গণতন্ত্রের ধ্যান-ধারণা হিসেবে; তখন প্রতিটি মতামত লোকসংখ্যার শক্তিশালী জাতির পক্ষে যাবে। অথবা পৃথিবীটা শাসিত হবে প্রকৃতির শক্তি বন্টনের মাধ্যমে; সেক্ষেত্রে সেইসব জাতিই জয়ী হবে, যারা নির্দয় এবং আত্মবঞ্চনায় রাজী হয়নি।
কারোর হয়ত বা এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে এ পৃথিবীতে একদিন অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রতিদ্বন্দীতায় মনুষ্য জাতির মধ্যে বীভৎস সংগ্রাম শুরু হয়ে যাবে। শেষে মানবতাবোধের আগুন গলাধঃকরণ করার পূর্বে, যা একমাত্র নির্বোধ ভীরুতা এবং বৃথা
অহংকারের সমন্বয়ে গঠিত, একদিন তা মার্চের প্রখর রৌদ্রতেজে গলে যাবে। মানুষ। মহান হয়েছে নিত্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পথ চলার জন্য, এ চিরস্থায়ী শান্তিতে তার সে মহত্ব নিচে নামতে বাধ্য।
আমাদের অর্থাৎ জার্মানদের পক্ষে ‘অর্ন্ত উপনিবেশ’ কথাটাই ভয়ানক; কারণ এটা আমাদের বিশ্বাস করতে উৎসাহিত করবে যে আমরা আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি বিশ্বজনীন শান্তিবাদ অনুসারে একটা পথ খুঁজে পেয়েছি এবং যা আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজন তা জোগাড় না করে অর্ধ-নিদ্রিত অবস্থায় অস্তিত্ব রক্ষা করে চলবে। এ শিক্ষা যদি আমাদের লোকেরা মনেপ্রাণে মেনে নেয়, তবে পৃথিবীতে আমাদের জন্য নির্দিষ্ট সঠিক জায়গা আর কিছুতেই খুঁজে বার করতে পারব না। যদি গড়পড়তা জার্মান একবার এ নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে পড়ে যে এ পদ্ধতিতেই সে তার প্রয়োজনীয় জীবন-যাপন এবং ভবিষ্যতের নিরাপত্তা খুঁজে পাবে, তবে সে আর কিছুতেই গা হাত পা নেড়ে লাভজনক জীবন-যাপনের পথ মাড়াবে না। তখন আমাদের দেশের সামনের সবচেয়ে মূল্যবান এবং বড় প্রশ্ন বাঁচার সংগ্রামটাই নিরর্থক হয়ে দাঁড়াবে। জাতি কি এটা মেনে নিয়ে মূল্যবান এবং প্রয়োজনীয় বৈদেশিক নীতিকে মৃত কবরের সমতুল্য বলে মনে করে তাদের আশাভরা ভবিষ্যতও হেলায় দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।
আমরা যদি উপলব্ধি করতে পারি যে ‘অর্ন্ত উপনিবেশ’ তত্ত্বের ফলাফল মাত্র একটা ঘটনা নয়, তাহলে আমাদের বুঝতে কষ্ট হবে যে এ ক্ষতিকর চিন্তাধারা যারা আমাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছে, তাদের প্রথম সারিতে রয়েছে ইহুদীরা। সে তার নিজের কোমলতার কথা ভালভাবেই জানে। কিন্তু বুঝতে অক্ষম যে প্রতিটি নোংরা কাজের শিকার হল তারা; যেটা ওপর থেকে সোনা মোড়া প্রতিশ্রুতির মত লোভনীয় মনে হয়। যা প্রকৃতিকে শ্রেষ্ঠতর কৌশলে পরাজিত করবে এবং তাদের অতিরিক্ত কিছু এনে দেবে — যার সাহায্যে তারা এ নির্দয় অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে জয়ী হতে পারবে। শেষ পর্যন্ত সম্রাট বলে নিজেদের কল্পনায় ভেবে নেবে; যখন সুযোগ অল্প কিছু কাজ করার, তা হাসিমুখে করবে।
এটা জোর করে বলা যায় না যে জার্মান অর্ন্ত উপনিবেশ স্থাপন করতে হলে প্রথম সামাজিক অভাব অভিযোগগুলো দূর করতে হবে। অন্ত উপনিবেশন পদ্ধতির প্রথম ধাপে জমিগুলোকে মুক্ত করে স্বাধীন করতে হবে; কিন্তু এটাই একটা জাতির ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট নয়; তাকে নতুন জমি দখল করতেই হবে।
অবশেষে যদি ভিন্ন পদ্ধতি বেছে নিই, তবে দেখতে পাব জমিগুলো এমন একটা পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে, যখন তার বেশি ফসল উৎপাদন এদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে জনশক্তির চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছে যাবে জাতি, যার থেকে তাকে আর বাড়ানো যাবে না।
অবশেষে নিচের বক্তব্যগুলো রাখা উচিত :
এটা সত্যি যে অন্ত উপনিবেশ স্থাপন একটা সীমাবদ্ধ ব্যবস্থা; জাতীয় সীমার সীমাবদ্ধ অবস্থায় সে জমির পরিমাণ তুলনায় খুবই কম এবং তার ফলে জননক্ষম কার্যক্ষমতাকেও সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য–এ দুটো জিনিস জাতির সাময়িক এবং রাজনৈতিক জীবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করবে।
কতখানি পর্যন্ত জাতীয় সীমা প্রয়োজনে তা স্থির হবে জাতির বহিঃশক্তি কি পরিমাণে শক্তিশালী। জমির পরিধি যত বড় হবে, জাতির আত্মরক্ষার সুযোগও তত বেড়ে যাবে। সামরিক তৎপরতা অনেক বেশি সত্বর, সহজে এবং অনেক বেশি পরিপূর্ণভাবে নেওয়া সম্ভব হবে যদি বিরুদ্ধ জাতির জমির পরিমাণ সীমাবদ্ধ হয়। অপরদিকে যে রাষ্ট্রের জমির পরিমাণ বেশি তাদের বিপক্ষে সামরিক অভিযান চালানোও কষ্টকর। উপরন্ত সীমা বহু বিস্তৃত হলে ভয় থাকে না যে চট করে অপর কোন জাতি সে দেশ আক্রমণ করার দায়িত্ব নেবে। কারণ সেক্ষেত্রে সংগ্রাম অনেক দীর্ঘতর এবং জয় বিলম্বিত হওয়ায় বিরুদ্ধ পক্ষের শক্তি নিঃশেষিত হয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। সেই আক্রমণের দায়িত্ব এত বেশি যে খুব বিশেষ কারণ না থাকলে বহিঃ আক্রমণ কেউ করবেই না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সীমান্তের ওপর জাতির স্বাধীনতা বহুল পরিমাণে নির্ভরশীল। অপরদিকে যে জাতির জমির সীমা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, আক্রমণকারীরা তার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাবেই।
সত্যি বলতে কি, জার্মান রাষ্ট্র এ দুটো কারণ এবং তার ফলাফল নিয়ে কখনই চিন্তা করেনি, তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রেখে সীমান্তটাকে সেই তুলনায় বাড়িয়ে যেত। অবশ্য এর কারণগুলোর আমি যে ব্যাখ্যা দিয়েছি তার চেয়ে অনেক আলাদা। কয়েকটা নৈতিক চারিত্রিক কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে রোধ করার চেষ্টা করা হয়নি। অন্ত উপনিবেশ স্থাপনের প্রস্তাবও রোষবশতই বাতিল করা হয়, কারণ তাদের ছিল এ ধরনের কোন ব্যবস্থা বড় জমিদারের স্বার্থে আঘাত হানবে। এ ধরনের আঘাত ব্যক্তিগত মালিকানায় প্রচণ্ড আঘাত হানার অগ্রগামী দূত হিসেবে কাজ শুরু করবে।
পরবর্তী সমস্যার সমাধান অর্থাৎ অন্ত উপনিবেশ সম্পর্কে যা কিছু কথা হয়েছিল তা শুধু বড় জমিদারের সংশয় উদ্রেক করার জন্য।
কিন্তু যে উপায়ে উপনিবেশ স্থাপনের প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল তা খুব কৌশল সম্পন্ন ছিল না। বিশেষ করে এ বাতিলের প্রশ্ন জনসাধারণের ওপর তার গভীর প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। যাহোক সমস্যার গভীর মূল পর্যন্ত কখনই যাওয়া হয়নি।
মাত্র আর দুটো পথ খোলা ছিল, যাতে এ বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ এবং রুটি জোগাড় হতে পারে।
তৃতীয়, নতুন নতুন জমি দখল করার চিন্তা করা উচিত ছিল, যাতে প্রতি বছরে এ নিত্য বর্ধিত জনসাধারণ বসবাস করতে পারে।
চতুর্থ, আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এভাবে সুসংগঠিত করা উচিত যাতে রপ্তানী বৃদ্ধি পায়, এবং বৈদেশিক ব্যবসা বাণিজ্যের লভ্যাংশের দ্বারা আমাদের জনসাধারণের ক্রয় ক্ষমতাও বাড়ানো যাবে, যা বর্ধিত জনসংখ্যাকে ভরণ-পোষণে সাহায্য করবে।
সুতরাং সমস্যাটা হল : কোন নীতি নেওয়া উচিত? দেশের সীমান্ত বাড়ানো অথবা উপনিবেশ স্থাপন, নাকি ব্যবসা বাণিজ্য। অনেক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিবেচনার পর দুটো নীতিকেই বাতিল করা হয়; এবং তার ফলে দ্বিতীয় পন্থাটাকেই বাছা হয়। অবশ্য সন্দেহ নেই প্রথমটাই ছিল অনেক বেশি বলিষ্ঠ নীতি।
নতুন জমি দখল করে সীমান্ত বাড়ানোর আদর্শ, যাতে বর্ধিত জনসংখ্যাকে বদলানো যেতে পারে, অনেক বেশি সুযোগ পাওয়া যাবে তাতে; বিশেষ করে আমরা যদি আজকের বর্তমানের সঙ্গে ভবিষ্যতের হিসেবটাকেও কষে দেখি।
প্রথমত এ ধরনের নীতি গ্রহণের জন্য খুব বেশি একটা গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয় যা। আমাদের কৃষক সম্প্রদায়কে জাতী সম্প্রদায়ের মধ্যে শক্তিশালী করে গড়ে তোলার জন্য। আমাদের বর্তমানের অনেক শয়তানীর মূল শিকড় হল পৌর গ্রাম্য জনসংখ্যার মধ্যের অসমতা।
আজকের সামাজিক ব্যাধিগুলোর বিরুদ্ধে ভালরকম ছোট এবং মাঝারী গোছের চাষীরা আশ্রয় পেয়ে এসেছে। উপরন্তু, ঘরোয়া জাতীয় অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে এটাই একমাত্র সমস্যা সমাধানের পথ, যার দ্বারা জাতি প্রত্যেক নাগরিকের নিত্যকার ক্ষুধার রুটি জোগাতে পারে।
এ অবস্থা যদি একবার বহাল করা যায়, তবে ব্যবসা বাণিজ্য তাদের অস্বাস্থ্যকর শীর্ষস্থান থেকে জাতীয় অর্থনীতির সাধারণ পদ্ধতি নিজের জায়গায় এসে স্থান নেবে, আজকের মত জাতীয় অর্থনীতিকে সাধারণ স্থান দখল করে বসে থাকবে না; চাহিদা এবং সরবরাহের মধ্যেও একটা সমতা বজায় রাখবে। এভাবে শিল্প এবং বাণিজ্য জাতীয় ভিত হিসেবে কাজ না করে, একটা সাহায্যকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করবে। তাদের যথাযথ কাজ চালিয়ে নিতে দিয়ে, জাতীর উৎপাদন এবং জাতীয় চাহিদার মধ্যে সমতা এনে দিলে এরা জাতির ভিত দৃঢ় করার কাজ স্বাধীনভাবেই করতে পারবে, যা প্রতিটি স্বাধীন দেশেই হয়ে থাকে। এবং জাতিকে মুক্ত এবং স্বাধীন রাখতেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। থাকবে, বিশেষ করে ইতিহাসের এ কুটিল সন্ধিক্ষণে।
এ সীমান্ত নীতি প্রাচ্যে সফল না হলেও একান্তভাবেই ইউরোপের জিনিস; একজনের স্থিরভাবে এবং সরাসরি এ সত্যের মুখোমুখি হওয়া উচিত। সর্বশক্তিময় ঈশ্বর তার বন্টনের রাজ্যে একটা জাতিকে অপর জাতির থেকে কখনই পঞ্চাশ গুণ বেশি দেবে না। এ আজকের ব্যাপার পর্যালোচনা করে, কারোরই উচিত নয় রাজনৈতিক সীমান্তকে চারিদিক থেকে টানাটানি করে শক্ত বিচারবুদ্ধির আদর্শগুলোর থেকে বিচ্যুত হওয়া। এ পৃথিবীতে যদি সবার প্রচুর পরিমাণে বসবাসের জায়গা নির্দিষ্ট থেকে থাকে, তবে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অংশটুকু আমাদের বুঝে নেওয়া উচিত।
অবশ্যই স্বতঃপ্রণোদিতভাবে জায়গা কেউ ছেড়ে দেবে না। ঠিক এ জায়গায় আত্মসংরক্ষণের নীতি তার কাজ করবে। এবং যখন বন্ধুত্বপূর্ণ উপায়ে এ সমস্যাগুলো সমাধান করা সম্ভব হবে না, দৃঢ় মুষ্টিতে তা ধরতে হবে যা বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করতে দেয়নি। অতীতে যদি আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা আজকের মত শান্তিবাদী বোধহীনতায় নির্ভর করে থাকে, তবে আমাদের আজকের বা সীমান্ত তার তিনভাগের এক ভাগের বেশি পাওয়া উচিত নয়, এবং সম্ভবত তাহলে ইউরোপে তার ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার জন্য আর কোন জার্মানই অবশিষ্ট থাকবে না।
আমরা আমাদের সাম্রাজ্যের দুই সীমান্তের কাছে ঋণী, জার্মান, অস্ট্রিয়া হল দক্ষিণের পূর্ব সীমান্ত এবং ইষ্ট প্রুশিয়া হল উত্তরে পূর্ব সীমান্ত, যা আমাদের পূর্ব পুরুষেরা অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে নিরপেক্ষভাবে স্থির করেছিল। এবং এ সগ্রামের মধ্যেই আমরা আমাদের অন্তশক্তির বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছি, যা আমাদের শুধু জাতিগত এবং রাজনৈতিক সীমান্ত বজায় রাখতেই সাহায্য করেনি, আজ পর্যন্ত আমাদের অস্তিত্বও বজায় রেখেছে।
অনেক সমকালীন ইউরোপীয় দেশগুলো পিরামিডের মত তাদের শৃঙ্গের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এ সব দেশের ইউরোপের সীমান্ত আশ্চর্যজনকভাবে ছোট, যখন তাদের উপনিবেশ এবং বৈদেশিক ব্যবসা বাণিজ্যের বোঝার সঙ্গে তুলনা করা হয়। অবশ্য এ প্রসঙ্গে এটা বলা চলতে পারে যে তাদের শৃঙ্গ ইউরোপে থাকলেও ভিত্ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে রয়েছে। ঠিক আমেরিকার উল্টো, যার ভিত্ রয়েছে আমেরিকা মহাদেশে আর শৃঙ্গ ছুঁয়ে রয়েছে সারা পৃথিবীতে। যা আমেরিকাকে অতুলনীয় অন্তশক্তি এনে দিয়েছে। এবং অপরদিকে এর উল্টো অবস্থার জন্যই ইউরোপের উপনিবেশ স্থাপনকারী শক্তিগুলো এত দুর্বল।
এ চিন্তাধারার বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ডের বলার কিছু থাকতে পারে না। যদিও বৃটিশ সাম্রাজ্যের মানচিত্রের ওপর চোখ বুলালে অনেকেরই হয়ত সমগ্ৰ অ্যাংলো-স্যাক্সন পৃথিবীটা নজর এড়িয়ে যাবে। ইংল্যান্ডের অবস্থার সঙ্গে ইউরোপের অন্যান্য কোন রাষ্ট্রের তুলনা চলে না; কারণ যে বিশাল সংস্কৃতি এবং বিভিন্ন ভাষার উপাদানে এ মহাদেশের সামাজিক পটভূমিকা গঠিত তার সঙ্গে একমাত্র আমেরিকারই তুলনা চলে।
সুতরাং জার্মানিকে যদি বলিষ্ঠ সীমান্ত নীতি কাজে পরিণত করতে হয়, তবে ইউরোপে তাকে নতুন জায়গা দখল করতে হবেই। উপনিবেশগুলো কখনই এ উদ্দেশ্য সফল করতে পারবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত সেগুলো বৃহৎ ভাবে ইউরোপীয়ানদের বসবাসের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। উনবিংশ শতাব্দীতে এ ধরনের কলোনী শান্তিপূর্ণ উপায়ে দখল করার কোন উপায় ছিল না। তাই এ ধরনের উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করার অর্থ ই ছিল প্রচুর পরিমাণে সামরিক প্রস্তুতি। সেই কারণে সামরিক সংগ্রাম ইউরোপের মধ্যেই জায়গা দখল করা সাগরের ওপারে কোন জমি দখল করার চেয়ে অনেক বেশি বাস্তব সম্মত ছিল।
অবশ্য এ মতবাদের জন্য প্রয়োজন জাতির একত্রিত শক্তি এ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা; এ ধরনের নীতি সফল করার জন্য এতে জড়িত প্রত্যেকের প্রতি আনন্দ, উৎসাহ এবং শক্তির প্রয়োজন, কখনই হেলাফেলায় চিত্তবিক্ষিপ্ত অবস্থাতে এর রূপায়ণ সম্ভব নয়। জার্মান সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক নেতৃত্ব সেই সময়ে এর উদ্দেশ্য সফলের নিমিত্তে নিয়োজিত করা উচিত ছিল। এ কাজ সম্পাদন করার আগে আর কোন কাজে হাত দেওয়া উচিত হয়নি। এবং এর সম্পাদনা সুচারুরূপে শেষ করার উপায় খুঁজে বার করাই ছিল এ নেতৃত্বের প্রধান কাজ।
জার্মানির এ সত্য উপলব্ধি করা উচিত ছিল যে এ ধরনের কাজ একমাত্র যুদ্ধ দ্বারাই সম্পাদন করা সম্ভব; সুতরাং সেই যুদ্ধে আগে থেকে সবরকম সংকল্প নিয়ে নামা উচিত ছিল।
পুরো মৈত্রী সম্পর্কটার মুখোমুখি এবং মূল্যায়ণ করা উচিত ছিল এ দৃষ্টিকোণ থেকে, যদি ইউরোপে নতুন অঞ্চল অধিকার করতেই হত, তবে তা করা উচিত ছিল রাশিয়ার জমি থেকে, এবং নতুন জার্মান সাম্রাজ্যের সেই আগেকার রাস্তাতেই চলা উচিত ছিল, যে একদা টিউটনিক নাইটদের পদাঘাতে লাঞ্ছিত। এবারে অবশ্য জার্মান লাঙলের জন্য জমি জার্মান তরবারী দিয়েই দখল করতে হবে, যাতে জাতিকে তার নিত্য প্রয়োজনীয় রুটি সরবরাহ করা যায়।
এ নীতি সফলভাবে রূপায়ণের জন্য ইউরোপের মাত্র একটা দেশের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করা উচিত। সেটা হল ইংল্যান্ড।
একমাত্র ইংল্যান্ডের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনের দ্বারাই এ নতুন জার্মান ধর্ম-যুদ্ধে তার রথের পেছনের চাকা রক্ষা করতে সমর্থ। এ অভিযানের স্বপক্ষে যুক্তি এত বলিষ্ঠ, পূর্ব পুরুষেরা। এর বিপক্ষে যেসব যুক্তি দেখিয়েছে সেগুলো অত নির্ভরশীল মোটেই নয়। পূর্বদেশের অধিকৃত জমিতে উৎপাদিত শস্যের দ্বারা তৈরি রুটি খেতে শান্তিবাদীরা কখনই গররাজী হবে না, যদিও প্রথম লাঙলকে ব্যবহার করতে তরবারী হিসেবেই বলা হয়েছে।
কোন ত্যাগই মহান নয়, যদিও ইংল্যান্ডের বন্ধুত্বের নিমিত্ত এটা প্রয়োজন। উপনিবেশ এবং নৌ-শক্তিতে একছত্র সম্রাট হওয়ার স্বপ্ন দেখা পরিত্যাগ করা উচিত এবং বৃটিশ শিল্পের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাটাও উচিত হবে না।
একমাত্র সুস্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট নীতির সাহায্যে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব। এ নীতি অবশ্য পৃথিবীর বাজার জয়ের চেষ্টাটাকে পরিহার করতে বলবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে উপনিবেশ স্থাপন এবং নৌ-যুদ্ধে শক্তিমান হওয়ার আশাটাকেও পরিত্যাগ করতে হবে। রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি এ স্থল যুদ্ধে নিয়োজিত করার আবশ্যক। এ নীতি বলিষ্ঠ এবং মহান ভবিষ্যতের জন্য বর্তমানে কিছুটা আত্মত্যাগ স্বীকার করতে বলবে।
এমন এক সময় ছিল যখন ইংল্যান্ড এ বিষয়ে আমাদের সঙ্গে একটা রফায় আসত; ইংল্যান্ড ভালভাবেই বুঝেছিল, নিয়ত জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে জার্মানির সমস্যাটা। ইংল্যান্ডের সাহায্যে ইউরোপে অথবা পৃথিবীর অন্য কোন প্রান্তে তার জমি দখল নিতান্তই প্রয়োজন।
এ দৃষ্টিভঙ্গিই হয়ত বা এ শতাব্দীর শেষে লন্ডনকে জার্মানির এত কাছাকাছি টেনে এনেছিল।
এ প্রথম জার্মানির মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যার পরিণতি নেহাত-ই করুণ। লোকে এ অসুখী ধারণা নেয় যে পরে হয়তো বা আমরা ইংল্যান্ডের কাছে তাদের বাদাম আগুন থেকে উদ্ধার করে দেওয়ার জন্য তৈরি থাকবে। এ যেন একটা মৈত্রী সম্পর্ক, শুধু দেওয়া নেওয়ার পরিবর্তে আর যে কোন বিষয়ের ওপর নির্ভর করে বেড়ে উঠতে পারে। এবং ইংল্যান্ডকেও সেই পারস্পরিক দর কষাকষির দলে ফেলা যায়। ব্রিটিশ কুটনীতিজ্ঞরা তখনো যথেষ্ট বুদ্ধিমান, যে কাজ ইতিমধ্যেই করেছে, তারা জানে এর সমতুল্য প্রাপ্তি আসন্ন।
ধরে নেওয়া যাক, ১৯০৪ সালে আমাদের জার্মানদের বৈদেশিক নীতি অত্যন্ত ধূর্তামির সঙ্গে পরিচালিত হয়েছিল, যা জাপানীদের সঙ্গে আমাদেরও অংশগ্রহণে বাধ্য করে। এর ফলাফলের তীব্রতা সহজে বোঝা সম্ভব নয়, যার ফলাফল জার্মানিকেই ভোগ করতে হয়েছিল।
মহাযুদ্ধ না হতেই ১৯০৪ সালে যা রক্তপাত হয়েছে–১৯১৪ পর্যন্ত তার এক দশমাংশ রক্তপাত হত কিনা সন্দেহ। এবং আজকে পৃথিবীর মানচিত্রে জার্মানি কত উঁচুতে স্থান পেত।
যে কোন শর্তে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে মৈত্রীর বন্ধন তখন অসম্ভব ছিল।
এ গলিত শবের মত রাষ্ট্রটা কখনই জার্মানির সঙ্গে নিজেকে জড়াত না যুদ্ধের উদ্দেশ্যে। বরং চিরস্থায়ী শান্তি বজায় রাখত, যার দ্বারা ধীরে ধীরে জার্মানদের এ দ্বৈত রাজতন্ত্রের থেকে নির্মূল করা যায়।
চরিত্রের এ অস্বাভাবিকতার আরেকটা দিক হল জার্মান জাতীয় স্বার্থরক্ষায় ওরা কখনই সক্রিয়ভাবে পাশে এসে দাঁড়াত না। কারণ তখন ওরা নিজেরাই উপলব্ধি করত যে নিজেদের নীতি, অর্থাৎ নিজেদের সীমান্তের ভেতরেই জার্মানদের নির্মূল করার কাজ চালিয়ে যাওয়া ওদের পক্ষে সম্ভব নয়। যদি জার্মানি নিজেরাই দৃঢ় জাতীয় মনোভাবের সাহায্যে এবং যথেষ্ট পরিমাণ নির্দয়তার সঙ্গে এ হাবুসবুর্গ রাষ্ট্রের দশলক্ষ অধিবাসীর ভাগ্য নির্ধারণের খেলায় না জড়াত। তবে হাবুসবুর্গ কখনই মহান এবং সাহসী জার্মানদের মদত দিত না। পুরনো জার্মান রাষ্ট্রের মনোভাব অস্ট্রিয়ার প্রতি হল জাতির বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করার ক্ষমতার পরীক্ষার মত।
যাহোক, জার্মানদের ওপর নির্যাতনের নীতি অস্ট্রিয়াকে চালিয়ে যেতে দিতে কখনই উচিত হয়নি, বাধা দেওয়া দূরে থাক। বরং বছর বছর তা বেড়ে গিয়ে শক্তিশালীই হয়েছে। অস্ট্রিয়ার সঙ্গে মৈত্রীর মূল্যায়ণ সঠিক হত যদি সেখানকার জার্মানদের ওপরে তুলে ধরা যেত। কিন্তু তা করা হয়নি।
তারা স্বপ্ন দেখেছিল পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের; কিন্তু ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখে বিশ্বযুদ্ধের মাঝখানে তারা দাঁড়িয়ে।
এ শান্তির জন্য স্বপ্ন দেখার পেছনে এক গভীর অর্থ নিহিত ছিল, কারণ ওপরে উল্লিখিত তৃতীয় পথ অর্থাৎ ভবিষ্যৎ জার্মানির সম্প্রসারণকে বেছে নেওয়ার কথা কর্তব্যের মধ্যে ধরা হয়নি। ব্যাপারটা হল নতুন জমি দখল করে সীমান্ত বাড়ানো একমাত্র পূর্বদিকেই সম্ভব ছিল; কিন্তু তা করতে গেলে যুদ্ধ অনিবার্য, তখন তারা যে কোন মূল্যে শান্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে। জার্মানির এক সময়ের বৈদেশিক নীতির ধুয়া ছিল; জার্মান জাতির সংরক্ষণে যে কোন পথ বেছে নাও। এখন সেটার পরিবর্তন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কোন উপায়ে পৃথিবীর শান্তি রক্ষা করতে হবে। আমরা অবশ্য এর ফলাফল জানি। আমি এ বিষয়ের ওপর আরো বিশদভাবে পরে আলোচনা করব।
তবে আরেকটা বিকল্প পথ হল, যাকে আমরা চতুর্থ বলতে পারি। এটা হল শিল্প এবং পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্য, নৌ-শক্তি এবং উপনিবেশ স্থাপন।
এ ধরনের উন্নতি অনেক তাড়াতাড়ি এবং সহজে করা সম্ভব। কোন জায়গায় উপনিবেশ স্থাপন এক অতি ধীর গতিসম্পন্ন পদ্ধতি; প্রায়ই সেটা পুরো শতাব্দী জুড়ে করতে হয়। তবু বলতে হবে, এর জন্য প্রয়োজন অন্তশক্তির। হঠাৎ অতি উৎসাহের বশে এ কাজ করা কখনই সম্ভব নয়, বরং ধীরে ধীরে অনেক বাধা বিঘ্ন সহ্য করেই এটা করা যায়, যা শিল্প উন্নতির চেয়ে একেবারে ভিন্ন। শিল্পোন্নতি কয়েক বছর সময়ের মধ্যে বিজ্ঞাপনের দ্বারা করা সম্ভব। অবশ্য এর ফলাফল খুব একটা দৃঢ় ভিত্ সম্পন্ন হয় না। বরং দুর্বল, যাকে সাবানের বুদবুদের মত ক্ষণস্থায়ী বলা যেতে পারে। নতুন সীমান্ত অধিকার করে সেখানে কৃষক বসিয়ে কৃষি কাজের জন্য ক্ষেত প্রস্তুত করার চেয়ে একটা পুরো নৌ-বহর গড়ে তোলা অনেক বেশি সহজ কাজ।
কিন্তু একথাও সত্যি যে পুরো নৌ-বহর ধ্বংসও কৃষিক্ষেত্রের চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি হয়। এ পদ্ধতিকে অনুসরণ করার অর্থই হল আজ হোক কাল হোক জার্মানিকে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া, এটা জার্মানির বোঝা উচিত ছিল। একমাত্র ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষেই বিশ্বাস করা সম্ভব যে মিষ্টি এবং তৈলাক্ত মধুর সম্ভাষণ অবিরত অকপট স্বীকার দ্বারাই তাদের কলার ভাগ পেতে পারে, যা তারা ধরে নিয়েছিল জাতিগুলোর বন্ধুত্বের বিনিময়ে পাবে, এবং তার জন্য কখনো তাদের যুদ্ধে নামতে হবে না।
একবার আমাদের এ পথ বেছে নেওয়ার অর্থই হল আজ হো কাল হো ইংল্যাণ্ড আমাদের শত্রু হতে বাধ্য। অবশ্য আমাদের বোকার মত ধারণার সঙ্গে এটা ঠিক খাপ খেয়ে গিয়েছিল। তবুও আমাদের ঘৃণা-মিশ্রিত রোষ বাড়ানো এর দ্বারা অমূলক ছিল। সত্যি বলতে কি, এমন একদিন এল যখন ব্রিটিশ আমাদের শান্তি প্রিয়তার মোকাবিলা করল নির্দয় চরম হিংস্র স্বার্থবাদীতার মাধ্যমে।
স্বাভাবিকভাবেই আমরা এ কাজ কখনই করতাম না।
রাশিয়র বিরুদ্ধে ইউরোপের সীমান্ত দখল নীতি সফল করা সম্ভব হত যদি আমরা ইংল্যান্ডের সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারতাম। অপরদিকে একমাত্র রাশিয়ার সাহায্যেই উপনিবেশ স্থাপন এবং পৃথিবীব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্য করা সম্ভব ছিল। কিন্তু সে ক্ষেত্রে এ নীতির আগাগোড়া ফলাফল ভেবে সচেতন মন নিয়ে গ্রহণ করা উচিত। সবচেয়ে আগে যেটা প্রয়োজন অস্ট্রিয়াকে সবার আগে বাতিল করা।
শতাব্দীর শেষে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে মৈত্রী প্রকৃত অর্থেই সমস্ত দিক থেকে নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়।
কিন্তু ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনের কথা কেউ চিন্তা করেনি, তেমনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য ইংল্যান্ডের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপনের কথাও কেউ ভাবেনি। কারণ উভয়ক্ষেত্রেই ফলাফল গিয়ে যুদ্ধে পরিণতি লাভ করত এবং একমাত্র যুদ্ধ এড়াতেই শিল্প এবং বাণিজ্য নীতিকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। এটা তৎকালে বিশ্বাস করা হয়েছিল, যে শক্তির সাহায্যে চিরদিনের জন্য পৃথিবী জয়ের বদলে ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা পৃথিবীটা জয় করা সম্ভব; এবং এটা শান্তিপূর্ণ নীতিও বটে।
অবশ্য মাঝে মাঝে এ নীতিটা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ যে থাকত না, তা নয়। বিশেষ করে বেশ কয়েকবার যখন ইংল্যান্ডের দিক থেকে ধারণার অতীত সাবধান বাণী উচ্চারিত হল, — এ কারণেই নৌ-বহর তৈরি করা হয়েছিল। ইংল্যান্ডকে আক্রমণ বা লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্য নয়। একমাত্র পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের মতবাদটাকে সংরক্ষণের নিমিত্তে,–যা ওপরে বলা হয়েছে, এবং সেই শান্তিপূর্ণ উপায়ে পৃথিবীটা জয়ের উদ্দেশ্যেই এ কাজ করা হয়েছিল। সে কারণে এ নৌ-বহর একটা নির্দিষ্ট পরিসীমার মধ্যে ধরে রাখা হয়েছিল। নৌ সংখ্যা এবং ওজনের দিক থেকে নয়, যুদ্ধার্থে প্রস্তুতির দিক থেকেও। এ উদ্দেশ্যের পেছনে এ নীতিই কাজ করেছে। আমরা প্রমাণ করতে তৎপর যে এ নৌ-বহরের সৃষ্টি শান্তি স্থাপনের জন্য প্রয়োজন,–যুদ্ধের কারণে নয়।
বাণিজ্যিক উপায়ে শান্তিপূর্ণভাবে পৃথিবী জয়ের ব্যাপারটা সম্ভবত রাষ্ট্রের আদর্শ পরিচালনার ব্যাপারে সবচেয়ে নিরর্থক বড়। এ নিরর্থক ব্যাপারটা বোকামীর চরম পর্যায়ে ওঠে যখন ইংল্যান্ডকে এ ব্যাপারে উদাহরণ হিসেবে দেখিয়ে বলা হয় যে ব্যাপারটা বাস্তবে কিভাবে প্রয়োগ করতে হয়। ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের মতবাদ এবং রাজ্য সম্বন্ধে আমাদের তথাকথিত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ধ্যান-ধারণা অপূরণীয় ক্ষতি করেছে এবং আমাদের লোকেরা না বুঝে কিভাবে ইতিহাস শেখে। সত্যি বলতে কি, বাণিজ্যিক উপায়ে পৃথিবীটা জয়ের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ড হল যুক্তিপূর্ণ উদাহরণ। ইংল্যান্ড ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন জাতি বাণিজ্যিক উপায়ে পৃথিবী জয়ের জন্য তরবারী ধরেনি এবং অপর কোন জাতি এত নির্দয়তার সঙ্গে এ বিজয়কে সংরক্ষণও করেনি। ব্রিটিশ রাজনীতি বিদ্যা বিশারদদের কি এটা চারিত্রিক গুণ নয়, যে তারা জানে রাজনৈতিক শক্তিটাকে অর্থনীতির সাফল্যে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, এবং বিপরীতভাবে অর্থনীতির সাফল্যটাকে রাজনীতির শক্তি হিসেবে কিভাবে ব্যবহার করতে হয়? কি বিস্ময়র ভূল এটা ভেবে নেওয়া যে ইংল্যান্ড তার নিজস্ব অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের জন্য নিজের রক্ত ঢালবে। ইংল্যান্ডের নিজস্ব জাতীয় সৈন্যদলে এ সত্যের কোন মূল্য নেই। সেই ব্যাপারে এ মুহূর্তে এটা সামরিক প্রধান রাজ্যও নয়, বরং হাতের কাছে যা সৈন্য পাওয়া যায় তা দিয়ে কাজ সারে–মনের জোরে আর গন্তব্যে পৌঁছনোর স্থিরতায়। ইংল্যান্ডের প্রয়োজন মাফিক সৈন্য দল সবসময়ই ছিল এবং আছে। সে সবসময়েই যুদ্ধ করে এসেছে সেইসব অস্ত্র দিয়ে যা যুদ্ধ জয়ের জন্য প্রয়োজনীয়। যতক্ষণ পর্যন্ত পর্যাপ্ত বেতন দেওয়া সম্ভব, ততক্ষণ পর্যন্ত বেতন ভোগী সৈন্যদলের সাহায্যেই সে লড়ে এসেছে। কিন্তু যখন আত্মত্যাগের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে–সেই মুহূর্তে বিজয়ের জন্য জাতির রক্ত ঢালতে সে কসুর করেনি। এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে এ সগ্রাম করার ইচ্ছা, একগুয়ে মনস্থিরতা এবং নির্দয় সামরিক ব্যবহার একভাবে বজায় রেখেছে।
এ অসংগতিপূর্ণ ধ্যান ধারণা ধীরে ধীরে কিন্তু যত্নের সঙ্গে জার্মান জীবনের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে গেছে। এ অবমূল্যায়ণের জন্য আমাদের ভাল মতই জরিমানা দিতে হয়েছে; এ প্রবঞ্চনা এত গভীরে যে ইংরেজদের আমরা ধূর্ত ব্যবসায়ী হিসেবে ঘৃণাই করে এসেছি; এবং ব্যক্তিগতভাবে ধরে নিয়েছি এরা অবিশ্বাস্যভাবে অতি নিচু ধাপের কাপুরুষ। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের ইতিহাসের গর্বিত শিক্ষকরা তাদের ছাত্রদের কাছে এ সত্য কখনই উদঘাটিত করেনি যে শুধুমাত্র প্রতারণা আর জোচ্চুরি দ্বারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মত এতবড় একটা সাম্রাজ্য কখনই গড়ে তোলা সম্ভব নয়। যে কয়েকজনের চোখে পড়েছিল এ সত্য, হয় তারা চুপ করে থেকেছে, নয় এড়িয়ে গেছে। আমি স্পষ্ট স্মরণে আনতে পারি আমার কয়েকজন সহকর্মীর মুখাবয়ব, যখন তারা যুদ্ধক্ষেত্রে গোরা সৈন্যদলের প্রতাপ দেখে বোকার মত পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করেছে। কয়েকদিন যুদ্ধের পর আমাদের সৈন্যরা উপলব্ধি করে যে এ স্কটগুলো ঠিক তাদের মত নয়, যা জার্মানরা এতদিন ধরে বলে এসেছে বা ব্যাঙ্গাত্মক বর্ণনাকারীর পর পত্রিকায় এবং সরকারি ইস্তাহারে প্রকাশ করেছে।
এ সময়েই আমি প্রথম এ বিভিন্ন ধরনের প্রচার ব্যবস্থাগুলোর যোগ্যতা বিচার করি।
এ মিথ্যা প্রকাশ, যারা বুঝিয়েছিল তাদের উদ্দেশ্য সাধন করে। ইংরেজদের প্রতি এ ব্যঙ্গ, যা মিথ্যা হলেও শান্তিপূর্ণ উপায়ে বাণিজ্য দ্বারা যে পৃথিবী জয় সম্ভব সেই ধারণার সহায়ক হয়েছিল। ইংরেজরা যেভাবে সফল হয়েছে, আমাদের সাফল্যও সেইভাবে আসবে। আমাদের অনেক বেশি সাধুতা এবং স্বাধীনতা তথাকথিত বিশ্বাসঘাতক ইংরেজদের থেকে অনেক বড় সম্পদ যা আমাদের পক্ষের শক্ত হাতিয়ার। সুতরাং ধরে নেওয়া হয়েছিল যে ছোট ছোট জাতের মহানুভূতি এবং শক্তিশালী জাতিবর্গের অবস্থা আমাদের পক্ষে অর্জন করা খুব সহজেই হবে।
আমরা উপলব্ধি করিনি, যে আমাদের সাধুতা অন্যদের আমাদের প্রতি বিরূপ করে তুলেছে, কারণ আমরা নিজেরাই এটাতে বিশ্বাস করিনি। বাকি পৃথিবীটা আমাদের ব্যবহারকে ধূর্ত প্রবঞ্চনাপূর্ণ ব্যবহারের প্রকাশ বলে ধরে নেয়; কিন্তু যখন বিপ্লব আসে তখন বিস্ময়ে তারা দেখে যে আমাদের মানসিক ভাবধারা আন্তরিকতাপূর্ণ হলেও নিবুদ্ধিতার সীমার বাইরে।
একবার যদি আমরা বুঝতে সক্ষম হই যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বাণিজ্য দ্বারা পৃথিবী জয়ের কল্পনা কতখানি নিরর্থক, তবে আমরা স্পষ্ট অন্য বিষয় ত্রি-পাক্ষিক মৈত্রীর নিষ্ফলতাও উপলব্ধি করতে পারব। কি অবস্থায় এ মৈত্রী গড়ে তোলা হয়েছিল? অস্ট্রিয়ার সঙ্গে মৈত্রীতে, এমন কি ইউরোপেও আমাদের পক্ষে সীমান্ত বাড়ানো সম্ভব হয়নি। এ সত্যটাই ত্রি-পাক্ষিক মৈত্রীর ভেতরকার দুর্বলতা। একজন বিসমার্ক তার নিজের কিছু প্রয়োজনের বদলে অন্য জিনিস ব্যবহার করতে সক্ষম, কিন্তু তার কদর্য উত্তরাধিকারীদের পক্ষে এটা কখনই সম্ভব নয়, এবং সর্বোপরি বিসমার্ক যে ভিতের উপর ত্রি-পাক্ষিক মৈত্রী গড়ে তুলেছিল, তার যখন আর কোন অস্তিত্বই নেই।
বিসমার্কের সময়ে তবু অস্ট্রিয়াকে জার্মান রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করা চলত; কিন্তু ধীরে ধীরে সার্বজনীন ভোটাধিকার পূর্ব শুরু হওয়ার পর দেশটা সংসদীয় হট্টগোলের জায়গায় পরিণত হয়, যেখানে জার্মানদের কণ্ঠস্বর কদাচিৎ শোনা যেত।
জাতিগত নীতির দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে এ মৈত্রী সর্বনাশা। একটা নতুন শ্লাভ মহাশক্তি জার্মান সাম্রাজ্যের সীমান্ত বরাবর জেগে ওঠে। উদাহরণস্বরূপ এ শক্তির জার্মান সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা রাশিয়ার থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। এ মৈত্রী তাই শূন্যগর্ভ এবং দুর্বল হতে বাধ্য; কারণ এর সদস্যরা তাদের ক্ষমতা হারিয়ে একে একে সরকারি অফিসগুলো থেকে দূরে সরে যেতে থাকে।
ঊনবিংশ শতাব্দীর কাছাকাছি অস্ট্রিয়ার সঙ্গে এ মৈত্রীর সম্পর্কটা ঠিক অস্ট্রিয়া আর ইতালির মৈত্রী সম্পর্কের পর্যায় এসে দাঁড়ায়।
এখানেও একমাত্র একটাই বিকল্প ছিল; হয় হাবুসবুর্গ রাজতন্ত্রকে সমর্থন জানানো, না হয় অস্ট্রিয়াতে জার্মানির নির্যাতনের প্রতিবাদ করা। কিন্তু বিশেষভাবে বলতে গেলে কেউ যদি এ পথ ধরে এগোয়, শেষপর্যন্ত তা গিয়ে শেষ হবে প্রকাশ্য সংঘর্ষে।
মনস্তত্বের দিক থেকেও এ ত্রি-পাক্ষিক মৈত্রীর মূল উদ্দেশ্য আত্মরক্ষার ব্যবস্থা হ্রাস করা। অথচ অপরপক্ষে এ ধরনের মৈত্রীর উদ্দেশ্যই হল পরস্পরের শক্তি সংযোজন করা, যে দল যত বাড়বে ততই তা বাস্তবে লক্ষ্য বস্তুর প্রতি সম্প্রসারণ হওয়া উচিত। এখানেও সর্বক্ষেত্রের মত সংরক্ষণে শক্তির প্রকাশ নয়, আক্রমণই হল সত্যিকারের শক্তির পরিচয়।
এ সত্য অন্যান্যরা উপলব্ধি করলেও তথাকথিত সংসদীয় সদস্যরা দুর্ভাগ্যবশত তা বুঝতে সক্ষম হয়নি। ১৯১২ সালের প্রথমপাদে লুডেনডর্ফে যে সামরিক বাহিনীর কর্ণেল এবং অফিসার ছিল, একটা স্মারকলিপিতে মৈত্রীর এ দুর্বল দিকটাকে তারা তুলে ধরে। কিন্তু রাষ্ট্রনেতারা সেই দলিলের কোন রকম গুরুত্ব দেয় না। সাধারণভাবে মনে হয়, এ ধারণা মানুষদের কাছে প্রযোজ্য, কিন্তু উন্নততর প্রজাতি যারা কুটনীতিজ্ঞ নামে পরিচিত, তাদের ক্ষেত্রে এ ধারণা অচল।
জার্মানির ভাগ্য বলতে হবে যে ১৯১৪ সালের যুদ্ধ সোজাসুজি এ কারণে অস্ট্রিয়ার সঙ্গে বাধে যার জন্য হাবুসবুর্গ এ যুদ্ধে অংশ নিতে বাধ্য হয়। যদি এ যুদ্ধের শিকড় অন্যরকম হত জার্মানিকে তার নিজের ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে একা ফেলে দিত। হাবুসবুর্গ কখনই এমন কোন যুদ্ধে নিজেকে জড়াত না বা অংশ নিতে রাজী হত না যার শিকড় জার্মানিতে; অথবা যে যুদ্ধের জন্য জার্মানি দায়ী। এক্ষেত্রে যেসব অবমাননাকর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, অস্ট্রিয়াও সেই পথেই যেত। সোজা কথা বলতে গেলে, যদি জার্মানিকে নিজস্ব কোন কারণে যুদ্ধে নামতে হত তবে অস্ট্রিয়া তার নিজের স্বার্থরক্ষায় অর্থাৎ যাতে কোনরকম বিপ্লব না বাধে, তার জন্য যুদ্ধ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকে নিরপেক্ষ রাখত।
শ্লাভেরা জার্মানিকে সাহায্যের অনুমতি দেওয়ার চেয়ে ১৯১৪ সালেই এ দ্বৈত রাজতন্ত্রকে গুঁড়িয়ে দিত; কিন্তু সেই সময়ে অতি অল্প সংখ্যক মুষ্টিমেয় লোকই বুঝতে পেরেছিল এ দানুবিয়ান রাজতন্ত্রের সঙ্গে মৈত্রীর বিপদ।
প্রথমত অস্ট্রিয়ার শক্ৰসংখ্যা অনেক ছিল যারা সাগ্রহে এ জীর্ণ শীর্ণ রাষ্ট্রটাকে পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে দখল করার তালে ছিল; সুতরাং এরা ধীরে ধীরে জার্মানির প্রতি একধরনের তীব্র ঘৃণা পোষণ করতে শুরু করে। কারণ জার্মানি হল এ দ্বৈত রাজতন্ত্র ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ার পথের একমাত্র বাধা। এ দ্বৈত রাজতন্ত্র লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ুক এটাই ওদের আশা এবং এ ব্যাপারে তাদের তীব্র স্পৃহা ছিল। ওদের ধারণা গড়ে ওঠে যে বার্লিনের মধ্যে দিয়েই একমাত্র ভিয়েনাতে যাওয়া সম্ভব।
দ্বিতীয়ত, এ নীতি গ্রহণ করে জার্মানিকে অন্যান্যদের সঙ্গে মৈত্রী গড়ার সবচেয়ে ভাল সুযোগ নষ্ট করে। এসব সম্ভাবনার বদলে যে কেউ অনুভব করতে পারত জার্মানির সঙ্গে রাশিয়া, এমনকি ইতালিও সম্পর্কের একটা টানাপোড়েন চলেছে। এবং এসব সত্ত্বেও এটা সত্যি যে অস্ট্রিয়ার প্রতি রোমের মনোভাব বিদ্বেষ ভাবাপূর্ণ হলেও, জার্মানির প্রতি তাদের ধারণা বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল। এ শত্রু পক্ষীয় মনোভাব প্রতিটি ইতালিয়ানের ভেতরেই সুপ্ত অবস্থায় ছিল, এবং যে কোন ছুতানাতায় তা ব্যাপকভাবে রূপ নিত।
বাণিজ্য এবং শিল্প নীতি গ্রহণ করায় রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের কোনপ্রকার ইচ্ছেই কারোর মধ্যে ছিল না। একমাত্র জার্মান এবং রাশিয়া, এ দেশের শত্রুরাই এ অবস্থায় ভেতরে যুদ্ধ বাধাবার জন্য সক্রিয় ছিল। সত্যি বলতে কি, একমাত্র ইহুদী এবং মার্কসীষ্টরাই উত্তেজিত করার চেষ্টা করত।
তৃতীয়ত, এ মৈত্রী নিরাপত্তার পক্ষে একটা চিরস্থায়ী বিপদ হয়ে দেখা দেয়। যে কোন বৃহৎ শক্তি যারা বিসমার্ক সাম্রাজ্যের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন ছিল তাদের পক্ষে সেই রাষ্ট্রগুলোর সৈন্য সমাবেশ করা সহজ ছিল, কারণ অস্ট্রিয়ার সঙ্গে মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হলে জার্মানকে লুণ্ঠন করার সুযোগ পাওয়া যাবে–স্রেফ প্রলোভনে লুব্ধ হয়ে।
অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ইউরোপের পূর্ব দেশগুলোকে একত্রিত করা কিছুমাত্র কঠিন কাজ ছিল না, বিশেষ করে রাশিয়া আর ইতালিকে। রাজা এডোয়ার্ডের নেতত্বে পৃথিবীর যেসব। দেশ সম্মেলনে যোগ দেয়, তা কখনই সত্যে পরিণত হত না, যদি না জার্মানির মিত্র অস্ট্রিয়া তাদের লুষ্ঠিত দ্রব্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এতটা প্রলুব্ধ না করত। এ সত্যটাই একমাত্র সম্ভব করে তুলেছিল এতগুলো রকমারি রাষ্ট্রের পাঁচ মিশেলি, যাদের স্বার্থ একটা বিন্দু থেকে নানাদিকে বিচ্ছুরিত, যা তাদের সবাই মিলে একটা সৈন্যশ্রেণী সুসংবদ্ধ করতে সাহায্য করেছে। প্রতিটি সদস্য কল্পনা করছে অস্ট্রিয়ার খরচায় নিজেদের ধনী করতে পারবে যদি তারা জার্মান আক্রমণে অংশগ্রহণ করে। তুকী পর্যন্ত এ দুর্ভাগ্যজনক মৈত্রীর মৌন সমর্থকের দলে ভিড়ে জার্মানির বিপদটাকে বাড়িয়ে খুব বিপজ্জনক সীমায় নিয়ে গেছে।
ইহুদী আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থা এ টোপ স্রেফ জার্মানিকে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছিল। কারণ অন্যান্য দেশের মত জার্মানি ব্যবসা বাণিজ্যের দিক থেকে কখনই তাদের নেতৃত্বকে মেনে নেয়নি।
এ উপায়েই অনেকগুলো রাষ্ট্রকে এক জায়গায় জড়ো করা হয়েছিল যাতে অন্ততপক্ষে দলে ভারী হওয়া যায়, যা দৈহিক সংঘর্ষের শিঙ বিশিষ্ট সীগফ্রীডের* সঙ্গে কাজে লাগবে।
হাবুসবুর্গ রাজতন্ত্রের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্কে অস্ট্রিয়া থাকাকালীন আমি অত্যন্ত ঘৃণা করতাম এবং ব্যাপারটা গভীরভাবে আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল; নিজের সঙ্গে অবিরত বোঝাপড়ার চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত আমি এ উপসংহারে আসি যা আগে বলেছি।
যে ছোট্ট গোষ্ঠীর মধ্যে আমি যোরাফেরা করতাম, সেখানেও আমি আমার মনোভাব গোপন করিনি যে এমন একটা রাষ্ট্রের সঙ্গে এ দুর্ভাগ্যজনক চুক্তি, শুধু দুঃখ কষ্ট পাওয়ার জন্যই যার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত। যদি জার্মান তার থেকে মুক্ত না হয়, তবে তার ভাগ্যে মহাদুর্ঘটনা ডেকে আনবে। আমি এক মুহূর্তের জন্যও সেই অভিমত থেকে সরে দাঁড়াই নি। এমন কি বিশ্বযুদ্ধের ঝড় যখন কার্যকারণের জাহাজটাকে ভগ্নাবশেষ করে দিয়ে তার কার্যক্ষমতা প্রায় শেষ করে এনে তার জায়গায় নিয়েছে অন্ধ উৎসাহ, এমন কি সেই গোষ্ঠীর মধ্যেও শীতল এবং শক্ত বিষয়ের প্রতি বস্তৃতান্ত্রিক চিন্তাধারা আন্দোলিত হতে শুরু করেছে। ট্রেঞ্চের মধ্যেও এ সমস্যাগুলোর অবতারণা হলেই আমি বেশ উঁচুস্তরেই আমার মতামত তুলে ধরতাম। আমার অভিমত ছিল যে জার্মানি যদি হাবুসবুর্গ সাম্রাজ্যের সঙ্গে তার সম্পর্কচ্ছেদ করে, তবে তার ক্ষতি কিছু হবে না, বরং শত্রু কমবে। লক্ষ লক্ষ জার্মান শিরস্ত্রাণ পরেছিল একটা দুর্নীগ্রিস্ত রাজবংশকে রক্ষা করার জন্য নয়, জার্মানদের পরিত্রাণের জন্য।
যুদ্ধের আগে একদল জার্মানের অস্ট্রিয়ার সঙ্গে জার্মানির এ মৈত্রী সম্পর্কে সামান্য সংশয় ছিল; মাঝে মাঝে জার্মান গোঁড়া গোষ্ঠী এ মৈত্রীর ওপর বেশি আত্মবিশ্বাস রাখার বিরুদ্ধে সাবধান বাণী উচ্চারণ করত। কিন্তু অন্য অন্য উপদেশাবলীর মত এটাকেও হাওয়ায় ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল। সাধারণের ধারণা হল পৃথিবী জয়টা সমুচিত, তাতে আত্মত্যাগ নামমাত্র, কিন্তু সাফল্য প্রচণ্ড।
আবার একবার অদীক্ষিত মানুষগুলোর করার কিছু ছিল না, শুধু সোজা ধ্বংসের দিকে হেঁটে চলা ছাড়া এবং তাদের প্রিয়জনকে একই কাজ করতে প্রলুব্ধ করত, যেমন করে ইঁদুরগুলো হ্যামলিনের বাঁশীওয়ালাকে অনুসরণ করছিল।
আমরা যদি গভীরভাবে ব্যাপারটাকে পর্যালোচনা করি যা পৃথিবী জয়ের অনর্থক কল্পনা এতগুলো লোকের কাছে সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছে, যে ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে পৃথিবী জয় সম্ভব, এবং জাতির চরম লক্ষ্য এটাই হওয়া উচিত। আমরা খুঁজে দেখলে দেখতে পাব যে এটা দেহ মনের ব্যাধি থেকে উৎপন্ন যা জার্মান রাজনৈতিক চিন্তার দেহটাতে অনুপ্রবেশ করেছিল।
প্রযুক্তি বিজ্ঞানের জার্মানিতে বিজয় এবং জার্মান শিল্পের চমৎকার প্রগতি এবং সমৃদ্ধি বাণিজ্য আমাদের ভুলিয়ে দিয়েছিল যে একটা শক্তিশালী রাষ্ট্র হয়ে ওঠার পক্ষে এগুলো পূর্ব-আবশ্যক।
উপরন্তু নির্দিষ্ট গোটাকয়েক গোষ্ঠী তত্ত্বটার অনুভূতি সম্পর্কে প্রকাশ করতে শুরু করে যে একটা রাষ্ট্রের অস্তিত্ব এসব অদ্ভুত ব্যাপারের ওপরেই নির্ভরশীল। সর্বোপরি অর্থনৈতিক স্বার্থ দেখার জন্য একটা অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান করা উচিত। সুতরাং তারা এ অভিমতেই আসে যে অর্থনৈতিক গঠনশীলের ওপর রাষ্ট্র নির্ভরশীল। এ ব্যাপারটাকে গৌরবান্বিত করে দেখা এবং বলিষ্ঠ আর, স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া হয়।
এখন সত্য হল যে একটা রাষ্ট্রের ব্যক্তিগতভাবে কোন অর্থনৈতিক ধ্যান ধারণা বা প্রগতির ব্যাপারে করণীয় কিছু নেই। এটা পরস্পর প্রতিদ্বন্দী দলের থেকে উদ্ভূত কোন আঁটসাঁট ব্যবস্থা বা অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য কোন সীমাবদ্ধ পরিসীমা। রাষ্ট্র হল বেঁচে থাকা প্রাণীদের একটা সামাজিক ব্যবস্থা যা গোষ্ঠীর শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক ব্যবস্থার প্রতিপালন করে থাকে, এবং সময়োচিত আয়োজন দ্বারা সে সেইসব জাতি বা শাখার শুধু অস্তিত্বই বজায় রাখে না; লালন পালনও করে। অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আরো কয়েকটা সহায়ক পথের মত একটা পথ মাত্র। কিন্তু তাই বলে অর্থনৈতিক কার্যকলাপই রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য বা মেরুদণ্ড নয়, যদি তা না মিথ্যা এবং অতিপ্রাকৃত কোন বস্তুর ওপরে তার ভিত হয়ে থাকে। এবং এটাই ব্যাখ্যা করার পক্ষে যথেষ্ট যে এ কারণেই কোন রাষ্ট্রকে কোন নির্দিষ্ট সীমান্তের ভেতরে থাকতেই হবে, এমন কোন কারণ নেই যা রাষ্ট্রের উন্নতির একটা কারণ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এ শর্ত হল অত্যাবশ্যক তাদের কাছে যারা তাদের জাতিবর্গকে তাদের সত্তা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেবে তাদের শিল্পের মাধ্যমে, এর অর্থ হল তারা তাদের কর্মের মাধ্যমে তাদের অস্তিত্ব রক্ষায় সচেষ্ট।
যে সব লোক তাদের পথ থেকে গোপনে সরে গিয়ে অন্যের রাজনৈতিক দেহে পরগাছার মত অপরের দ্বারা নিজেদের কাজ করিয়ে নেয় বিভিন্ন রকমের ভাগ করে, তারা যে রাষ্ট্র গড়বে সেই রাষ্ট্রে কোন নির্দিষ্ট সীমার প্রয়োজন নেই। এটা বিশেষ করে কোন পরগাছা জাতির ক্ষেত্রে প্রয়োজন, বর্তমান সময়ে যারা মনুষ্যত্বের সততার দিকটার দোহাই পাড়ে; আমি অবশ্য সেই ইহুদীদের সম্পর্কে বলছি।
ইহুদী রাষ্ট্র কখনই একটা সীমার মধ্যে ছিল না। এটা সমস্ত পৃথিবী ব্যাপী ছড়ানো, কোথাও কোন সীমান্ত ছাড়া। সব সময়ই তাদের সদস্যরা বিশেষভাবে একটা জাতির থেকেই এসেছে। সেই কারণেই ইহুদীরা সর্বদা রাষ্ট্রের ভেতরে রাষ্ট্র তৈরি করেছে। একটা প্রধান প্রতিভাশালী কৌশল হল যা সব সময় অভিসন্ধিমূলক, ইহুদীরা তাদের রাষ্ট্র নামক জাহাজটাকে সব সময় ধর্মের ধ্বজা উড়িয়ে নিয়ে গেছে, কারণ বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাস সম্পর্কে আর্যদের বিশ্বাস অপরিসীম। কিন্তু এ কারুকার্যময় আইনের অর্থ আর কিছুই নয়, এ মতবাদের আড়ালে নিজেদের অর্থাৎ ইহুদী জাতির সংরক্ষণ। সুতরাং এ আইন তাদের সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনৈতিক বিজ্ঞান, সব ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়েছে শুধু লক্ষ্যে পৌঁছবার নিমিত্ত।
একটা প্রজাতির নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার সহজাত প্রবৃত্তি হল তাদের সামাজিক সংগঠন করার প্রাথমিক কারণ।
সুতরাং রাষ্ট্র হল জাতিগত যান্ত্রিক গঠন, অর্থনৈতিক কোন সংস্থা নয়। এ দুটি বিষয়ের পার্থক্য এত বেশি যে ব্যাপারটা ধারণার অতীত যা আমাদের সমকালীন রাষ্ট্রনেতারা বোঝে না। তার জন্য তারা মনে করে যে রাষ্ট্র একটা অর্থনৈতিক গঠনশৈলীর ওপরে নির্ভরশীল, কিন্তু সত্য ব্যাপার হল যে এটা উদ্ভূত হয়েছে প্রজাতি এবং জাতিবর্গের সংরক্ষণের চেষ্টা থেকে। কিন্তু এ গুণগুলো সব সময়েই কাব্য সংস্কৃতির ওপরে নির্ভরশীল, বাণিজ্যিক অহমিকায় নয়। প্রজাতিদের সংরক্ষণের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন একক ব্যক্তিত্বের আত্মত্যাগ। কবির নিচের কথাগুলোর মানেই হল :
যদি তোমার জীবনটাকে পণ না কর,
তবে তুমি তোমার জীবনটাকে জয় করতে পারবে না।
শিলার : ভ্যালেনস্টাইন।
একক ব্যক্তিত্বের অস্তিত্বের আত্মত্যাগ জাতির রক্ষায় অতি প্রয়োজনীয়। সুতরাং এটা হল জাতি স্থাপনে এবং সংরক্ষণের অতীব প্রয়োজনীয় একটা শর্ত, যা সমস্বার্থতা এবং একই জাতীয় চরিত্রের ওপরে নির্ভরশীল এবং একই বিষয়গুলো রক্ষণের নিমিত্ত যে কোন মূল্য দিতে স্থির সংকল্পে অবিচল থাকা দরকার। যে সব লোকেরা তাদের নিজেদের সীমান্তের ভেতরে বসবাস করে তারা স্বভাবতই এ কারণে তাদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং ছলচাতুরীর দিকটাই উন্নত করে, যদি না আমরা স্বীকার করি যে এ চরিত্র তাদের সহজাত এবং রাজনৈতিক ধরন ধারণের ওপর এত পরিবর্তন নির্ভর করে যা এ পরগাছা জাতির সহজাত অভিব্যক্তি।
রষ্ট্রের প্রথম অবস্থায় মানুষের চরিত্রের এ বীরত্বপূর্ণ দিকটায় অভিব্যক্তি প্রকাশ পায়, যা আমি আগে বলেছি। এবং যারা এ অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে পরাজিত হয়, অর্থাৎ যারা অধীনতা স্বীকার করে নেয়, আজ হোক কাল হোক তাদের অদৃশ্য হয়ে যেতেই হবে, এবং একই পথের পথিক তাদেরও হতে হবে যারা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বলিষ্ঠতা না দেখিয়ে অস্তিত্বরক্ষার সগ্রামে নামবে বা অহমিকার বৃথা চর্চায় মনোনিবেশ করবে। এসব ক্ষেত্রে পরাজয়ের কারণ বুদ্ধিমত্তার অভাবের জন্য নয়, সাহস এবং দৃঢ় সংকল্পের অভাবের জন্যই এটা হয়ে থাকে। এ ব্যাপারটাকে গোপন করার জন্য মানুষের অনুভূতি শক্তি বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়।
রাষ্ট্র সংগঠনের ভিত কখনই অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর দাঁড়িয়ে থাকে না। উপরন্তু, অর্থনীতির সঙ্গে এর সম্পর্ক অতি অল্প বা নেই বললেই চলে। এবং এটা সুস্পষ্ট যে রাষ্ট্রের অন্তর্নিহিত শক্তির সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্প্রসারণের একত্রে মিল খুব কমই থাকে। এর অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যখন দেখা যায় অর্থনৈতিক প্রগতি সত্ত্বেও রাষ্ট্র ধ্বংসের মুখে এগিয়ে চলেছে। মানুষের সামাজিক ব্যবস্থা অর্থনৈতিক উন্নতির সময়ে রাষ্ট্রের শক্তিও সর্বোচ্চ হওয়া উচিত। বরং উল্টো হওয়াই বিচিত্র।
বিশেষ করে এটা বোঝা অত্যন্ত কষ্টকর যে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক শক্তি দ্বারা সমৃদ্ধ এবং সংরক্ষণ করা সম্ভব এ বিশ্বাসের প্রচলন হয়, যদিও ইতিহাস এর বিরুদ্ধেই বারে বারে রায় দিয়েছে। প্রুশিয়ার ইতিহাসই পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে যে নৈতিক চালই একটা রাষ্ট্র গঠন করে, এবং তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপারে কোন ভূমিকা নেই। এ নৈতিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে অর্থনীতি উন্নতি করা সম্ভব এবং তা ফুলে ফেঁপে ওঠে যতদিন না পর্যন্ত সৃজনশীল রাজনৈতিক ক্ষমতা হ্রাস পায়। এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক গঠনশৈলীও ভেঙে পড়ে, যা আমাদের চোখের সামনে ভয়াবহভাবে ঘটে চলেছে। মনুষ্য জাতির বস্তৃতান্ত্রিক উন্নতি বলিষ্ঠ নৈতিকতার ছায়াতেই একমাত্র বেড়ে ওঠা সম্ভব। যে মুহূর্তে তাদের জীবনের প্রাথমিক ধ্যান ধারণা হিসেবে গণ্য করা হবে, সেই মুহূর্তেই তা তাদের অস্তিত্বটাকেই ধ্বসিয়ে দেয়।
যখনই জার্মানির রাজনৈতিক শক্তি বিশেষভাবে শক্তিশালী ছিল, তখনই অর্থনৈতিক অবস্থারও উন্নতি হয়েছে। কিন্তু যখনই মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক অবস্থা প্রধানতম স্থান নিয়েছে, তখনই জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শগুলোকে ঠেলে পেছনে সরিয়ে দিয়েছে; সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের ভিত্ ধ্বসে পড়ে পেছনে পেছনে অর্থনৈতিক ধ্বংসও ডেকে এনেছে।
আমরা যদি সৃষ্টি এবং সংরক্ষণের জন্য কি কি প্রয়োজন, এ প্রশ্নটাকে বিবেচনা করি, তাহলে দেখতে পাব :
কর্মক্ষমতা আর সবার উন্নতির জন্য একক ব্যক্তিত্বের আত্মত্যাগ–এ গুণগুলোর মধ্যে অর্থনীতির কোন সম্পর্কই নেই। একথা অতি সত্য, বৈষয়িক কোন উন্নতির জন্য মানুষ আত্মত্যাগ করে না। অন্য কথায় সে তার আদর্শের জন্য মৃত্যুবরণ করতে পারে, কিন্তু ব্যবসার জন্য নয়। জনসাধারণের মনস্তত্ত্বের চমকপ্রদ দিকটা যা ইংরেজরা মহাযুদ্ধের সময়ে তুলে ধরেছিল, আমার মনে হয় এর চেয়ে ভাল করে সাধারণের মনস্তত্ত্ব আর কেউ বুঝতে পারে নি। আমরা যুদ্ধ করেছিলাম রুটির জন্য; কিন্তু ইংরেজ ঘোষণা করে যে এটা তাদের মুক্তিযুদ্ধ। এবং তাও তাদের নিজেদের মুক্তির জন্য নয়। তারা তাদের ছোট্ট জাতির মুক্তির জন্য যুদ্ধ করে চলেছে। জার্মানরা ইংরেজদের এ দৃষ্টতায় হেসেছিল, এবং বলতে বাধা নেই মনে মনে ক্রুদ্ধও কম হয়নি। কিন্তু এভাবে তারা প্রমাণ করে দিয়েছিল যে আমাদের কূটনীতিজ্ঞদের মধ্যেও রাজনৈতিক সচেতনতা যুদ্ধের আগেই কত কমে গিয়েছিল, এ সব তথাকথিত কুটনীতিজ্ঞদের বিন্দুমাত্র ধারণাও ছিল না যে কী শক্তি মানুষকে স্বেচ্ছায় এবং দৃঢ় সংকল্পে মৃত্যুর মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়েছে।
১৯১৪ সালে যুদ্ধে যখন জার্মানরা বিশ্বাস করত যে তারা একটা আদর্শের জন্য যুদ্ধ করছে, ততদিন পর্যন্ত তারা দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে থেকেছে। যেইমাত্র বলা হয়েছে যে তারা দৈনন্দিন রুটিন তাগিদায় যুদ্ধ করছে, তক্ষুনি তারা যুদ্ধ পরিত্যাগ করে সরে দাঁড়িয়েছে।
ধূর্ত রাষ্ট্রনেতারা এ পরিবর্তিত অনুভূতিতে বিস্ময়াভূত হয়ে পড়ে। তারা একথাটা কখনই বুঝে উঠতে পারেনি যে যখন মানুষকে নিছক বস্তৃতান্ত্রিক কারণে ডাকা হবে, তখন তারা আপ্রাণ চেষ্টা করবে মৃত্যু এড়িয়ে যেতে; মৃত্যু এবং বৈষয়িক ফলশক্তির উপভোগ পরস্পর বিরোধী ধারণা। এমন কি দুর্বলতম মহিলাও নায়িকা হয়ে দাঁড়াবে যদি তার সন্তানের জীবন বিপজ্জনক অবস্থায় এসে দাঁড়ায়। সর্ব যুগে দেশ, জাতি এবং রাষ্ট্রকে রক্ষা করার তীব্র ইচ্ছাই মানুষকে তার শত্রুর অস্ত্রের মুখোমুখি দাঁড় করায়।
নিচের ব্যাপারগুলোকে সত্য বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে যা সব সময় ভাল বলে প্রতিপন্ন হয়েছে :
একটা রাষ্ট্রে অভ্যুদয় কখনই বাণিজ্যিক কারণে হয় না। এমন কি শান্তিপূর্ণ বাণিজ্যিক সেবাতেও নয়। রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের কারণ হল একটা গোষ্ঠীর প্রতিপালনের সহজাত প্রবৃত্তির থেকে। এ সহজাত প্রবৃত্তির অভিব্যক্তি বীরত্ব ব্যঞ্জক বা ছল-চাতুরী পূর্ণ, যা-ই হোক না কেন। প্রথম অবস্থায় আমাদের রাষ্ট্র ছিল আর্য রাষ্ট্র; যার ভিত্ ছিল কর্মের আদর্শে এবং সাংস্কৃতিক প্রসারতার ওপরে নির্ভরশীল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, আমাদের রাষ্ট্রে ইহুদীদের পরগাছা উপনিবেশে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু যে মুহূর্তে অর্থনৈতিক স্বার্থ জাতি প্রীতি এবং সংস্কৃতির ওপরে প্রভুত্ব বিস্তার করে, তালাক বা রাষ্ট্র যার ভেতরেই হোক না কেন, এ অর্থনৈতিক স্বার্থ এসব কারণগুলোকে আগা করে দিয়ে পরাভব এবং অত্যাচার ডেকে আনে।
যুদ্ধের পূর্বে জার্মানিতে এ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে জার্মানির পৃথিবী জয় একমাত্র বাণিজ্যিক এবং উপনিবেশ স্থাপনের মাধ্যমেই সম্ভব যা সত্যিকারের রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্য অর্থাৎ জাতির সংরক্ষণ এবং অত্যুদয় সেই লক্ষ্যেই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। সংকল্প, দূরদৃষ্টি, ও বাস্তবতার দ্রুত অবনতি হতে শুরু করে। যে গুণগুলো রাষ্ট্রের সঠিক উন্নতির প্রধান সোপান। মহাযুদ্ধ এবং এর ফলাফল এ গুণগুলোকে একেবারে দেউলিয়া করে ছাড়ে।
যারা ব্যাপারটাকে নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করেনি, তাদের কাছে জার্মানদের মনোভাব বিশেষভাবে অদ্রবণীয় হেঁয়ালী বলে মনে হয়েছে। সর্বোপরি, জার্মানি নিজেই একটা সাম্রাজ্যের সুন্দর উদাহরণ যা সম্পূর্ণ রূপে ক্ষমতার নীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। প্রাশিয়া, যা নাকি জার্মান সাম্রাজ্যের উৎপাদনক্ষম কোষ বলে পরিগণিত, তৈরি হয়েছিল নায়কোচিত কার্যকল্প দ্বারা। অর্থনৈতিক বা ব্যবসা বাণিজ্যের ওপর ভিত্তি করে নয়। এবং সম্রাট নিজে এ নেতৃত্বের চমৎকার যোগ্য ব্যক্তি, যে নেতৃত্বে ক্ষমতার নীতি এবং সামরিক শৌর্য বীর্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত।
তবে সেই একই জার্মানদের রাজনৈতিক সহজাত প্রকৃতির এতটা অধঃপতন হল কি করে? এটা শুধু একটা একক ব্যাপারের ওপর নির্ভর করে এ অবক্ষয়িত অবস্থায় এসে পৌঁছায় নি, দেহমনের ব্যাধি দ্বারা উৎপন্ন রোগাদির অসংখ্য লক্ষণ প্রচণ্ডভাবে রাজনৈতিক দেহে ফুটে উঠেছিল। যা জাতির দেহটাকেই কুরে কুরে খেয়ে ফেলেছিল বিষাক্ত ঘায়ের মত। মনে হচ্ছিল কেউ যেন অলক্ষ্যে এ নায়কোচিত দেহের রক্তে রহস্যজনক হাতে কোন বিষাক্ত তরল পদার্থ ঢুকিয়ে দিয়েছে, যা ব্যপ্ত হয়ে পড়েছে সর্বত্র। এবং ধীরে ধীরে ডেকে এনেছে শরীরের এ পঙ্গুতা, যার জন্য নিজেদের সংরক্ষণের সহজাত প্রবৃত্তিটাই হারিয়ে ফেলেছে।
১৯১২-১৪ সালে আমি এ সমস্যাগুলো নিয়ে নিত্য নিজের মনে তোলপাড় করতাম, যার সঙ্গে এ ত্রি-পাক্ষিক মৈত্রী এবং অর্থনৈতিক নীতি সম্পর্কটাকে সম্রাট অনুসরণ করত। আবার আমি এ মতে উপস্থিত হই যে এ হেয়ালীর একমাত্র কারণ হল সেই শক্তির প্রভাব যার সঙ্গে আমার পরিচয় ভিয়েনাতে। যদিও তা আমি অন্য ধরনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছি। যে শক্তির কথা আমি বলেছি তা হল মার্কসীয় শিক্ষা। সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি–সমগ্র জাতির মধ্যে যার পরিব্যাপ্তি।
আমি আবার দ্বিতীয়বার জীবনে এ বিধ্বংসী শিক্ষার গভীরভাবে বিশ্লেষণ করি। এবারে অবশ্য আমি আমার নিত্যকারের পরিবেশ এবং প্রভাব মুক্ত হয়ে বিশ্লেষণের তাগিদায় প্রশ্নটাকে বিচার বিবেচনা করিনি। বরং জার্মানির রাজনৈতিক জীবনের ব্যাপার স্যাপারগুলোর ওপরেই আমার পর্যবেক্ষণ সীমাবদ্ধ রেখেছি। এ নতুন পৃথিবীর তত্ত্বের দিকটা মানসিক কোদাল দিয়ে খনন করতে গিয়ে আমি এ শিক্ষানীতির সুস্পষ্ট ফলাফল দেখতে পাই, মার্কসীয় নীতির তাত্ত্বিক দিকটার সঙ্গে আজকের ঘটা সংস্কৃতি, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যাপারগুলোর তুলনা করি।
আমার জীবনে প্রথম আমি এ মহামারীর পরাজয়ের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি।
বিস্মার্কের অপূর্ব আইন প্রণয়ন প্রণালী অনুধাবন করি; এর ধ্যান ধারণা, প্রয়োগ এবং ফলাফল। ধীরে ধীরে আমার নিজস্ব মতামতের একটা দৃঢ় ভিত্তি গড়ে ওঠে, যা পাথরের ন্যায় দৃঢ়; যে কারণে ভবিষ্যতে সাধারণ সমস্যাগুলোর জন্য আর আমাকে মন পরিবর্তন করতে হয় নি। এর সঙ্গে সঙ্গে আবার আমি মার্কসিষ্ট এবং ইহুদীজাতির ভেতরকার সম্পর্কটা বিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করি।
আমার ভিয়েনায় প্রবাসের দিনগুলোতে জার্মানিকে আমি দেখতাম শান্ত বিশাল প্রতিমূর্তি বিশেষ। তবু মাঝে মাঝেই প্রচণ্ডরকমের সন্দেহ এবং অবিশ্বাস আমাকে অস্থির করে তুলত। নিজের মনে মনে এবং ছোষ্ট্র যে গোষ্ঠীর সঙ্গে আমি মিশতাম, জার্মান বৈদেশিক নীতি নিয়ে তাদের সঙ্গে আমি পর্যালোচনা করতাম এবং আমার চিন্তাধারায় মার্কসিস্টদের অবিশ্বাস্য আগা পথে তাদের প্রতি ব্যবহার করা হত; যদিও তখন। জার্মানির এটা একটা মূল সমস্যা ছিল। আমি বুঝতে পারি না এ চরম বিপদের মধ্যে কি করে তারা বদ্ধ চক্ষুবশত হোঁচট খেত, যার প্রতিক্রিয়া ছিল আবশ্যক যদি প্রকাশ্যে ঘোষিত মার্কসীয় নীতি বাস্তবে রূপায়িত করা হত; এমনকি সেদিন, অত শীঘ্র আমি আমাকে ঘিরে থাকা লোকদের সতর্ক করে দিয়েছিলাম, আমি বৃহত্তর দশককেও তাই করেছি যে এ সমস্ত শান্ত করা স্লোগান হল অলস এবং বিফল : আমাদের কিছু হবে না। এ একই ধরনের রোগের সংক্রমণে ইতিমধ্যেই বিরাট একটা সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে দিয়েছে। যে আইন সমস্ত মানবজাতিকে দাসে পরিণত করে, তার বাইরে কি জার্মানি যেতে পারবে?
১৯১৩-১৯১৪ সালে প্রথম আমি আমার মতামত বিভিন্ন গোষ্ঠীতে ব্যক্ত করি; যার মধ্যে কিছু সংখ্যক লোক এখন ন্যাশনাল স্যোশালিস্ট মুভমেন্টের সদস্য। কিভাবে জার্মান জাতি তার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা পেতে পারে তা নির্ভর করছে কিভাবে মার্কসীয় মতবাদকে নিমূল করা যাবে।
আমি বিশ্বাস করি ত্রি-পাক্ষিক মৈত্রীর সর্বনাশকর কার্যকলাপ হল মার্কসীয় শিক্ষার আংশিক প্রতিক্রিয়া; এ নীতি সবার অলক্ষ্যে বলিষ্ঠ রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ভিতে ফাটল ধরিয়ে দিয়েছে। যারা ঘন ঘন এ চিন্তাধারায় নিজেদের কলুষিত করেছে, তারা এ সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির থেকে উদ্ভুত বিপদ এবং তাদের উদ্দেশ্যটাকে ধরতে পারেনি; যদিও তা’ তারও আগে সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত ছিল, যা মাঝে মাঝে জাতির অস্তিত্বটাকেই বিনষ্ট করে টুকরো টুকরো করে দিতে উদ্যত হয়েছে। কখনো কখনো চিকিত্সার সাহায্যে রোগের লক্ষণগুলোকে তারা দূর করবার চেষ্টা করেছে, যা তাদের ধারণায় হল মূল কারণ। কিন্তু কেউ প্রকৃত রোগের কারণ বা তার শিকড়টাকে খুঁজে বার করার চেষ্টা করেনি। এ পথে মার্কসের নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেও কোন ফল না পেয়ে তারা স্রেফ হাতুড়ে বদ্যির মলম দিয়ে রোগ সারাবার প্রচেষ্টায় নেমেছে।
০৫. মহাযুদ্ধ
আমার যৌবনের কোলাহলপূর্ণ দিনগুলোতে কোন কিছুই আমার উদ্দাম চেতনাকে এত বেশি সঁতসেঁতে করে দিত না, একমাত্র একটা চিন্তা ছাড়া; সেটা হল— আমি এমন একটা সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলাম যখন নাকি পৃথিবী সুনিশ্চিতভাবে ঠিক করে ফেলেছে যে খ্যাতির মন্দির আর তৈরি করা চলে না। ব্যতিক্রম হিসাবে সম্মান দেখানো হবে একমাত্র ব্যবসায়ী এবং রাষ্ট্রের অফিসারদের। ঐতিহাসিক কর্ম সম্পাদনের ঝড় ইতিমধ্যেই বরাবরের মত থিতিয়ে এসেছে এতটা পরিমাণে যে ভবিষ্যৎ মনে হচ্ছে সঁপে দিয়েছে জাতিদের শান্তিপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, যার থেকে তাকে পুনরুদ্ধার বা সংশোধন করা অসম্ভব। এর সহজ সরল অর্থ হল পরস্পরের সাহায্যে পরস্পরকে শঠতাপূর্ণ প্রতারণা, আত্মরক্ষার্থে ও শক্তির আশ্রয় নেওয়ার ব্যাপারটাই যেন এর বাইরে। ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি দেশকে মনে হচ্ছিল এক একটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, জোর করে সীমান্ত বাড়ানো আর খদ্দেরের পরস্পরের প্রতি রেয়াত্ যে কোন ছুতানাতায় ব্যাপারটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। এবং এর আনুসঙ্গিক পদার্থ হিসাবে উঁচু গলায় গোলমাল অবশ্যই অনুপকারীরা করে চলেছিল। এ ব্যাপারটা নির্দিষ্ট খাতে স্থিরভাবে দিনে দিনে বরাবরের মত বেড়েই চলেছিল। জনসাধারণের অনুমোদন পেয়ে শেষমেষ এটা সমস্ত পৃথিবীটাকে সুবিশাল এক মনিহারী দোকানে পরিণত করে চলেছে। এ দোকানের দেউরিতে সারি সারি স্মারক আবক্ষ মূর্তি সাজানো যা এ মুনাফাখোরদের অমরত্বের সঙ্গে মিলানো, যারা নিজেদের ব্যবসার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ধূর্ত এবং সেইসব শাসকশ্রেণীর কর্মচারী যারা নিজেদের অত্যন্ত নির্দোষ বলে জনসাধারণের কাছে নিজেদের তুলে ধরেছে। বিক্রয়রত মানুষগুলো হচ্ছে ইংরেজ এবং শাসনকর্ম চালিয়ে যাওয়া লোকগুলো হল জার্মান। কিন্তু ইহুদীরা তাদের উৎসর্গ করবে এমন ব্যবসাতে যা লাভজনক না হলেও তা হতে হবে এক মালিকের; কারণ তারা প্রকাশ্যে সব সময় চিক্কার করবে যে তারা একেবারেই লাভ করছে না, আর তাদের পকেট থেকেই গুণাগার দিতে হচ্ছে সব সময়। উপরন্তু বিদেশী ভাষায় তাদের জ্ঞান থাকায় এ বাড়তি সুবিধেটুকুও তারা পেয়ে থাকে।
আমি কেন আরো একশ বছর আগে জন্ম নিলাম না? আমি নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করতাম। স্বাধীনতাযুদ্ধের কোন এক সময়ে যখন ব্যবসায়ী না হলেও মানুষকে কিছু মূল্য দেওয়া হত।
এভাবে আমি নিজেকেই ভাগ্যহীন বলে ভাবতাম যে দুর্ভাগ্যের কারণেই আমার এ পৃথিবীতে উপস্থিতি এত দেরিতে হয়েছে এবং একথা ভাবতেও আমার বিরক্তি লাগত যে আমার জীবনটা আমাকে শান্তিপূর্ণ এবং আদেশ মেনে চলে কাটাতে হবে। ছেলে হিসাবে আমি যা-ই হই না কেন, শান্তিবাদী ছিলাম না এবং নিজেকে সেই ধরনের তৈরি করার সমস্ত রকমের প্রচেষ্টা অসারে পরিণত হয়।
তখন দূর দিগন্তে বুয়র যুদ্ধ শুরু হয়েছে। হঠাৎ সংবাদপত্রে তা পড়তাম এবং প্রায় সব টেলিগ্রাম এবং সরকারি ইস্তাহারগুলোকে গোগ্রাসে গিলতাম। সবচেয়ে বেশি আনন্দ লাগত যে দূর থেকে হলেও এ যুদ্ধের আমিও একজন প্রত্যক্ষদর্শী।
যখন রুশ-জাপানী যুদ্ধ শুরু হয়, তখন আমার বয়সও যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি নিজের মধ্যেও বিচার বোধটা তীক্ষ্ম হয়েছে। জাতীয় কারণেই আলোচনার সময়ে আমি জাপানীদের পক্ষ নিতাম। রাশিয়ানদের পরাজয় যে অস্ট্রিয়ায় শ্লাভাজিমের প্রতি সজোরে মুষ্ট্যাঘাত।
ইতিমধ্যে বহু বছর কেটে গেছে যখন আমি মিউনিকে আসি। এখন আমি উপলব্ধি করতে পারি যে আগে যা বিশ্বাস করতাম, যা হল অবক্ষয়ী দেহমনের দ্বারা উৎপন্ন ব্যাধি, যা ঝড়ের পূর্বের শান্ত অবস্থা বজায় রেখেছিল। আমার ভিয়েনার দিনগুলোয় বকা সেই গুমোট ক্ষণিক বিরতির মুঠোয় ধরা পড়েছিল, যা অশনি সংকেতের পূর্ব লক্ষণই প্রদর্শন করেছে। এখানে সেখানে মাঝে মাঝেই বিদ্যুৎ চমক দেখা যেত; কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে তা নৈরাশ্যের অন্ধকারে অতি শীঘ্র মিলিয়ে যেত। এরপরেই বলকানের যুদ্ধ বেঁধে ওঠে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তার প্রধান অতিথিরূপে প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু প্রবল উত্তেজনাময় ইউরোপকে ঝটিকাগতিতে আচ্ছন্ন করে ফেলে। এ অতিরিক্ত শান্ত অবস্থায় মানুষ নিজেকে নির্যাতিত এবং ভাবী অমঙ্গলের সূচনা দেখতে পায়। এর তীব্রতা এত বেশি যে আসন্ন আকস্মিক দুর্ঘটনার ধারণাটা একটা অসহিষ্ণু আশায় পরিবর্তিত হয়। তাদের আশা ছিল যে ঈশ্বর তাদের ভাগ্যের বল্লাটাকে নিশ্চয়ই এবার আলগা করে দেবেন এতখানি যে সেই ভাগ্যকে কোন ঘটনাই আর দমন করতে পারবে না। ঠিক এ সময়ে বেশ বড় রকমের একটা বিদ্যুৎ চমক হঠাৎ এসে পৃথিবীটাকে চমকে দেয়। ঝড় ওঠে এবং স্বর্গের বজ্র নির্ঘোষের সঙ্গে মিশে যায় মহাযুদ্ধের কামানের গর্জন ধ্বনি।
আর্চ ডিউক ফ্রানজ ফার্দিনান্দের হত্যা সংবাদ যখন মিউনিকে এসে পৌঁছায়, — আমি সারাটাদিন বাড়িতেই বসে থাকি এবং সত্যি বলতে কি সমস্ত ব্যাপারটাকেই আমি ঠিক অনুধাবন করতে পারি নি। প্রথমে আমি আশংকা করেছিলাম যে কোন অস্ট্রিয়ান জার্মান ছাত্র হয়ত গুলিটা ছুঁড়েছে। হাবুসবুর্গ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী শ্লাভদের প্রতি পক্ষপাতিত্বপূর্ণ কার্যাবলীতে তার ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাই আর সে নিজেকে দমন করতে পারেনি। দেশের ভেতরকার শত্রুদের কাছ থেকে জার্মান লোকগুলোকে মুক্ত করার জন্যই হয়ত বা সে এ পথ বেছে নিয়েছে। এ ভুলের মাশুলের গুনাগারটা কী দিতে হবে তা সহজেই কল্পনা করা যায়। এটা আবার নতুন নির্যাতনের একটা ঢেউকেই ডেকে নিয়ে আসবে এবং পৃথিবীর সামনে তা সঠিক বলেই বিবেচিত হবে। কিন্তু অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি সেই গুপ্তঘাতকের নাম জানতে পারি, তাদের পরিচিতি ছিল শ্লাভ হিসেবে। আমি এক হতবুদ্ধিকর অনমনীয় প্রতিহিংসার অবস্থা অনুমান করি,–যা ভাগ্য তাকে নিয়ে যেতে কৃতসংকল্প। শ্লাভদের প্রিয়তম বন্ধু শ্লাভ দেশপ্রেমিকের গুলিতেই বিদ্ধ হয়েছে।
তখনকার ভিয়েনার সরকারের পক্ষে তখন অন্যায় সেই দিনের প্রচলিত ধারা অনুসারে যে চরমপত্র দেওয়া হয়েছিল তাকে দোষী সাব্যস্ত করে। একই ঘটনার এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর অন্য কোন সরকারই বিকল্প কোন অবস্থা গ্রহণ করতে পারত না। অস্ট্রিয়ার দক্ষিণ সীমান্তে এক নির্দয় শত্রু সদা সর্বদা উত্তেজনার খোরাক এ দ্বৈত রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে জুগিয়ে চলেছে নিয়মিত বিরতিতে; এবং সে বিরতি ক্রমেই নিকটতর হচ্ছে। এ অধ্যবসায়ের সঙ্গে এখনো কিছুতেই সাম্রাজ্য ধ্বংস না হওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত থামত না। অস্ট্রিয়াতে আশা ছিল বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সেই মুহূর্তটা এগিয়ে আসবে। একবার এটা করতে পারলেই রাজতন্ত্রের পক্ষে আর কোনরকম শক্ত প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়।
কয়েক বছর আগে পর্যন্ত রাষ্ট্র ফ্রানসিস্ যোসেপের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে সাধারণ বিরাট জনতার চোখে এ বৃদ্ধ এবং শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিত্বের মৃত্যু সম্রাটের মৃত্যুরই তুল্য। সত্যি বলতে কি শ্লাভ নীতির এ কৌশল হল অস্ট্রিয়ান রাষ্ট্র যাতে এ ধারণা পোষণ করে যে সম্রাটের বিরল প্রতিভা এবং আশ্চর্যজনক ঘটনাবলীর জন্যই এ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। এ ধরনের চাটুকারিতাই হাবুসবুর্গের পছন্দ ছিল। বিশেষত এর সঙ্গে সম্রাটের সত্যিকারের কার্যকলাপের কোন সম্পর্কই ছিল না। এ আরোপিত গৌরবের নিচেকার অন্ধকারে সাবধানে লুকিয়ে রাখা যন্ত্রণাটাকে আর কেউ খুঁজে বার করতে চেষ্টা করেনি। একটা সত্যকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল, মনে হয় ইচ্ছে করেই। যে সম্রাট যত বেশি পরিমাণে তার শাসনকার্যে পদস্থ কর্মচারীদের ওপর নির্ভর করেছে, ততই তারা আরো বেশি করে ‘সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট’ বলে তাকে তুলে ধরেছে; কিন্তু ভাগ্য যখন দরজায় এসে আঘাত করে তার রাজস্বের দাবি জানিয়েছে, তখনই আকস্মিক মহা দুর্ঘটনা নেমে এসেছে।
সেই বৃদ্ধ এবং শ্রদ্ধাস্পদকে বাদ দিয়ে কি অস্ট্রিয়ার সাম্রাজ্যকে কল্পনায় আনা যায়? তা হলে সঙ্গে সঙ্গে কি মারিয়া থেরেমার বিপর্যয় আবার সংঘটিত হবে না?
ভিয়েনার সরকারি বিভাগের পক্ষে সত্যি এটা অন্যায় যে তারাই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে দেশকে যুদ্ধে নামিয়েছিল, যা হয়ত বা প্রতিরোধ করা অসম্ভব ছিল না। যুদ্ধ অবশ্যই বাধত, তবে দু’এক বছর এটাকে পেছনো গেলেও যেতে পারত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ জার্মান বা অস্ট্রিয়ার কুটনীতিজ্ঞরা কেউ-ই সেই চরম দিনের হিসেবটা করতে পারেনি; সে কারণেই তাদের মুষ্ঠাঘাতও হয়েছে চরম সময়ে।
না। যাদের এ যুদ্ধে নামার ইচ্ছে ছিল, তাদের এর ফলাফল বহনে অস্বীকার করলে চলবে কেন? এর ফলাফল নিশ্চিতভাবেই হল অস্ট্রিয়াকে উৎসর্গ করা। এবং যদি যুদ্ধ, যুদ্ধ হিসেবেও না এসে পড়ত, — তবু সমস্ত জ্ঞাতিসমূহ একসঙ্গে মিলে আমাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ত, যা হাবুসবুর্গ সাম্রাজ্যকে খণ্ড খণ্ড করে তবে ছাড়ত। সেক্ষেত্রে অবশ্য আমাদের ঠিক করতে হতো আমরা হাবুসবুর্গের পাশে এসে দাঁড়াব, নাকি দূরে সরে থাকব হাতজোড় করে দর্শকের মত, যাতে ভাগ্য তার নিজস্ব গতিতে এগিয়ে যেতে পারে।
আজকে যারা আজকের অমঙ্গলের জন্য সরব এবং তাদের জ্ঞানের আড়ম্বর যুদ্ধের কারণ দর্শাতে ব্যস্ত,–সেই লোকগুলোর সহযোগীতাই এ সাংঘাতিক যুদ্ধের প্রতি দেশ ধাবিত হয়েছিল।
কয়েক যুগ ধরেই জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা ধূর্ত এবং নিচতার সঙ্গে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য আলোড়ন তুলে আসছে। কিন্তু জার্মান সেন্টার পার্টি, যাদের দৃষ্টিভঙ্গীর শেষ কথা হল ধর্ম; তাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অস্ট্রিয়া রাষ্ট্রকে সর্বপ্রধান করার,–যেখান থেকে জার্মান নীতি মোড় নিয়েছে।
এ পরিণতির মূখতার জন্ম এখনো হয় নি। যা এসেছে, তা আসতে বাধ্য; এবং কোন কিছুতেই তাকে প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। জার্মান সরকারের ভুল হল, একমাত্র শান্তিরক্ষার কারণে যে সমস্ত সুযোগগুলো তাদের স্বপক্ষে ছিল তারও সুযোগ তারা নেয় নি। শুধু পৃথিবী ব্যাপী শান্তির জন্য মৈত্রীর ফাদে পা বাড়িয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর সম্মিলিত শক্তিবর্গের শিকার হয়েছে–যারা জার্মানির এ শান্তি রক্ষার প্রচেষ্টায় বিরোধী ছিল, তারা আটঘাট বেঁধে যুদ্ধকে ডেকে নিয়ে এসেছে।
যদি তল্কালীন ভিয়েনা সরকার তাদের চরমপত্র এতটা তীব্র শর্তাবলী সম্বলিত নাও করত, তবু সেই পরিস্থিতির খুব একটা হেরফের হত বলে মনে হয় না। কিন্তু তা জনসাধারণের ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ জাগিয়ে তুলত। কারণ সাধারণ জনতার চোখে এ চরমপত্র এমন কিছু নিষ্ঠুর বা অতিরিক্ত ছিল না। যারা আজকে এ সত্যটাকে অস্বীকার করে, তারা হয় নির্বোধ নয় দুর্বল স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন অথবা ইচ্ছে করেই মিথ্যার বেসাতি করা মানুষ।
১৯১৪ সালের যুদ্ধ কোন মতেই জনগণের উপরে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয় নি; সত্যি বলতে কি জনসাধারণই এটা চেয়েছিল।
সাধারণের ভেতরের অনিশ্চয়তাকে একেবারে শেষ করার ধারণার বশবর্তী হয়েই এ চিন্তা করা হয়েছিল। এবং এ সত্যের আলোকে উদ্বুদ্ধ হয়েই দুই লক্ষ জার্মান যুবা স্বেচ্ছায়। এ রঙে নিজেদের রাঙিয়েছে এবং তারা এ সত্যের জন্য তাদের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত উৎসর্গ করতে রাজী ছিল।
আমার কাছে এ মুহূর্তগুলো যৌবনের দিনগুলোয় আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া দুর্দশার বোঝাটার মুক্তির সময় এনে দিয়েছিল। আজকে আমার স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে সেই মুহূর্তে আমি উৎসাহের বন্যায় ভেসে গিয়েছিলাম এবং আমার হাঁটু পর্যন্ত ডুবে গিয়েছিল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ আমাকে আজ পর্যন্ত সে ভার লাঘবের জন্য বাঁচিয়ে রেখেছেন।
এ মুক্তিযুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে অসমকরণভাবে ভেঙে পড়েছিল। যে মুহূর্ত থেকে ভাগ্য জাহাজের হাল ধরেছে, জনসাধারণের ভেতরে এ জনমত গড়ে ওঠেছে যে অস্ট্রিয়া অথবা সারভিয়ার ভাগ্য তাকে কোথায় নিয়ে চলেছে। কিন্তু জার্মান জাতির অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল।
অবশেষে অনেক বছরের অন্ধত্বের পরে লোকে পরিষ্কারভাবে ভবিষ্যতটাকে দেখতে পায়।
সুতরাং মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চাপা স্বরে পরিবর্তে অতিরিক্ত উত্তেজনার প্রাবল্য দেখা দেয়; কারণ এ উল্লাস নিছক বয়ে যাওয়া হঠাৎ উন্মত্ততা ছিল না। পরিস্থিতির গুরুত্ব বোঝাটা অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। সেই সময়ে কারোর সবিশেষ ধারণা ছিল না কতদিন ধরে এ যুদ্ধ চলবে। লোকে স্বপ্ন দেখত সৈন্যরা বড়দিনে ঘরে ফিরে আসবে এবং শান্তির সঙ্গে তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম আবার শুরু করবে।
মানব জাতির চরিত্র হল সে যা বিশ্বাস করে তা-ই আশা করে এবং তার ওপরে পরিপূর্ণ আস্থা রাখে। জনতার এ আচ্ছন্ন করা অনুভূতি ধীরে ধীরে চিরস্থায়ী অনিশ্চয়তায় অবসন্ন হয়ে পড়ে, বিশেষ করে জনসাধারণ যে ব্যাপারগুলোয় বিশেষভাবে জড়িত। সুতরাং কেউ ভাবে নি যে অস্ট্রিয়া সারভিয়ার সংঘর্ষ কুলঙ্গীতে তোলা থাকবে। সেই জন্যই তারা মৌলিক কোন হিসেব নিকেশ আশা করেনি। সেই লক্ষ লক্ষ ইচ্ছুক ব্যক্তিদের মধ্যে আমিও একজন ছিলাম।
যেইমাত্র সারভিয়া অত্যাচারের সংবাদ এসে মিউনিকে পৌঁছায়,–আমার মনের আকাশে তৎক্ষণাৎ দুটো চিন্তা ভেসে ওঠে : প্রথমত, যুদ্ধ অনিবার্য এবং দ্বিতীয়ত, হাবুসবুর্গ এবার তার মৈত্রী সংঘে স্বাক্ষরের সম্মান দিতে বাধ্য। আমি সবচেয়ে বেশি ভয় পেয়েছিলাম যে মৈত্রীর বন্ধনের দরুন একদিন জার্মানিকেও যুদ্ধে নামতে হবে এবং প্রথম ধাক্কা তাকেই সামলাতে হবে, অস্ট্রিয়াকে নয়। এ আকস্মিক ঘটনায় আমার মনে হয়েছিল অস্ট্রিয়া তার ঘরোয়া রাজনীতির জন্য মৈত্রীর পক্ষে দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু বর্তমানে সে বিপদ কেটে গেছে। পুরনো রাষ্ট্র বাধ্য হয়েছে সংগ্রামে লিপ্ত হতে। স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছাতেই হোক।
এ সংঘর্ষ সম্পর্কে আমার নিজের ধ্যান ধারণা সহজ এবং স্পষ্ট ছিল। আমার বিশ্বাস এ সংঘর্ষ অস্ট্রিয়ার সারভিয়াকে সন্তুষ্টির জন্য নয়; বরং জার্মানির নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রশ্নটাই যেন বড় হয়ে উঠেছে–জার্মান নীতির শুধু মুক্তির প্রশ্ন এটা নয়, — ভবিষ্যতের প্রশ্নও এ সংঘর্ষের সঙ্গে জড়িত।
বিসমার্কের অসমাপ্ত কাজ এবার শেষ করার পালা। আমাদের পিতৃ-পুরুষেরা বহু নায়কোচিত যুদ্ধে উইসেনবুর্গ থেকে শুরু করে সেদান এবং প্যারিতে যে রক্তক্ষয় করেছে, তার উপযুক্ত হতে হবে আজকের যুবক জার্মানদের। এবং এ সংগ্রামে যদি জার্মানরা জয়ী হতে পারে, তবে আবার জার্মান জাত জাতি হিসেবে পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতিদের সারিতে গিয়ে দাঁড়াবে। একমাত্র তখনই জার্মান সম্রাট তাকে শান্তির ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলে দাবি করতে পারে। এবং এ শান্তিরক্ষার জন্য তাদের দৈনন্দিন রুটির বরাদ্দও আর হিসেব করে করতে হবে না।
বালক এবং একজন যুবা হিসেবে আমি প্রায়ই এমন কোন ঘটনা খুঁজে বেড়াতাম যার মাধ্যমে আমার জাতীয়তাবাদী উৎসাহ যে উবে যায়নি তা দেখাতে পারি। জয়ের উল্লাসকে আমার যেন মাঝে মাঝে মনে হত প্রশ্রয়দানকারী পাপী, যদিও এ ধরনের অনুভূতির কোন কারণ দর্শানো আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ এ জয়ধ্বনিতে তাদেরই অধিকার, যাদের ভেতরে নাটকীয়তা নেই বা যেখানে ঈশ্বর জাতিকে সত্যের গন্তব্যে নিয়ে যেতে আদিষ্ট এবং মানুষকে কি তার সেই কঠিন পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে? লক্ষ লক্ষ মানুষের মত আমিও এ পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতির আনন্দে আনন্দিত ছিলাম। প্রায়ই আমি গান গেয়ে উঠতাম–জার্মান-দেশ হল সবার ওপরে। এবং সঙ্গে সঙ্গে ‘হাইল’ অর্থাৎ ‘জয় হোক’ বলে চিৎকার করতাম। সে সব অনুভূতির সত্যতা নিরূপণের জন্য প্রায়ই আমি অতীতের স্মৃতি রোমন্থন করে ঈশ্বরের বিচারশালায় উপস্থিত হতাম।
প্রশ্ন থেকেই একটা জিনিস আমার কাছে স্পষ্ট ছিল যে যুদ্ধ বাধলেই, যা আমার কাছে অবশ্যম্ভাবী বলে মনে হয়, আমার বইগুলো তৎক্ষণাৎ ঠেলে একপাশে সরিয়ে রেখে দেব। আমি আরো অনুভব করি যে আমার জায়গা হল সেখানে, যেখান থেকে আমি আমার অন্তরের আহ্বান শুনতে পাচ্ছি।
প্রধানত রাজনৈতিক কারণেই আমি অস্ট্রিয়া ছেড়েছিলাম। এর থেকে কি বেশি বিচারশক্তি সম্পন্ন হতে পারে যা আমার রাজনৈতিক ধ্যান ধারণা পরিবেশ অনুযায়ী যৌক্তিক হতে পারে। এখন সেই যুদ্ধই বেঁধে গেল। হাবুবুর্গের হয়ে যুদ্ধ করার কোন ইচ্ছেই আমার ছিল না, কিন্তু আমার জ্ঞাতিবর্গ এবং সম্রাটের জন্য মৃত্যুকেও আমি পরোয়া করি না।
৩ আগস্ট, ১৯১৪ সালে আমি মহানুভব রাজা তৃতীয় লুইভিগের কাছে ব্যাভেরিয়ার সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের অনুমতি প্রার্থনা করে একটা দরখাস্ত করি। তখনকার দিনে সম্রাটই ছিলেন সর্বেসর্বা। এবং দু’একদিনের ভেতরে উত্তরও পেয়ে যাই যে আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছে। আমি উত্তরটা পেয়ে কম্পিত হাতে খুলি এবং আজ তা ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা অসম্ভব যে আমি যখন পড়ে দেখি আমাকে ব্যাভেরিয়ার সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আমি যে খুব আনন্দিত হয়েছিলাম তাতে সন্দেহ নেই। কয়েকদিনের মধ্যে আমি সেই পোশাক গায়ে চড়াই, যা পরবর্তী ছ’ বছরে আর আমি খুলে রাখিনি।
আমার পক্ষে যা, সব জার্মানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় অধ্যায়ের সূচনা হয়। সেই সগ্রামের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, পেছনের ফেলে আসা স্মৃতির টুকরোগুলো সব বিস্মৃতির গর্ভে লীন হয়ে আসে। সতৃষ্ণ গর্বে আমি সেই দিনগুলোর দিকে ফিরে চাই, বিশেষ করে আমরা যখন সেই উল্লেখযোগ্য ঘটনার দশম বর্ষে পদার্পণের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি। আমার সেই যুদ্ধের প্রথম কয়েক সপ্তাহের স্মৃতি সব সময় স্মরণে আসে, যখন ভাগ্য আমাকে সেই নায়কোচিত সংগ্রামে জাতির মধ্যে ঠাঁই দিয়েছিল।
আমার মনের সামনে যখন দৃশ্যপটগুলো খোলা হয়, তখন মনে হয় যেন তা গতকালের ঘটনা। আমার মানস চোখে ভেসে ওঠে সেই দৃশ্যটা, যখন আমি আমার যুবক সহকর্মীদের সঙ্গে কুচকাওয়াজে রত এবং সেটা সীমান্ত ছাড়ার শেষ দিন পর্যন্ত আমরা করে এসেছি।
অন্য সবার মত একটা চিন্তাই আমাকে ভাবিয়ে তুলতো, তাহল আমাদের সীমান্তের যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছতে যদি দেরি হয়ে যায়। মাঝে মাঝে এ চিন্তা আমাকে উদ্বিগ্ন করে তুলত এবং প্রতিটি বিজয় ঘোষণা আমাকে তিক্ততার স্বাদ এনে দিত, যেটা পরবর্তী বিজয় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেকটা বেড়ে যেত।
অবশেষে সেই দিনটা উপস্থিত হল যখন আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য মিউনিক ছাড়লাম। জীবনে এ প্রথম আমি রাইন নদী দেখলাম; যখন আমরা পশ্চিমের দিকে অগ্রসর হচ্ছি সেই ঐতিহাসিক নদী চিরাচরিত এবং উদ্যত শক্রর গ্রাস থেকে রক্ষা করার সংকল্পে। সূর্যের প্রথম রশি হালকা কুয়াশা ভেদ করে মাটিতে পড়েছে এবং আমাদের সম্মুখে নীদারভালন্ডের প্রতিমূর্তি প্রকটিত, সৈন্যভর্তি ট্রেনটাই গেয়ে ওঠে,–রাইনের তীরে জেগে উঠলাম। আমি অনুভব করতে পারি যে আমার হৃদয় যেন সে উচ্ছ্বাস আর ধরে রাখতে পারছে না।
এবং তারপরেই এসে উপস্থিত হল ভিজে আর সঁতসেঁতে একটা রাত। সারাটা রাত আমরা নিঃশব্দে এগিয়ে চললাম, কুয়াশা ভেদ করে যেইমাত্র প্রথম সূর্যরশ্মি আমাদের সামনে এসে পড়ল, সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপরে সশব্দে বোমা ফাটার শব্দ। বোমা গোলা আমাদের মধ্যেই এসে পড়তে লাগল এবং তা ভিজে মাটির ওপরে ছত্রাকার। কিন্তু সেই বোমা গোলার ধোঁয়া অপসারিত হওয়ার আগেই দুশো কণ্ঠের সম্মিলিত এক জয়ধ্বনি। এটা মৃত্যুকে আলিঙ্গনের অভিব্যক্তি। তারপরেই শুরু হয় গুলির শিসধ্বনি আর কামানের গর্জন, যোদ্ধাদের চিৎকার চেঁচামেচি আর সমবেত কণ্ঠের গান। জ্বর হলে যেমন চোখ টাটায়, তেমনি টাটাচ্ছে, তবু আমরা এগিয়ে চলেছি। দ্রুতগতিতে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি এসে পৌঁছাই। পেছনে বীট পালং আর ঘাসের প্রান্তর। সত্বর গানের সুর আমাদের বহুদূরে নিয়ে যায়। ক্রমে ক্রমে সেই গানের সুর নিকটতর হতে শুরু হয়। প্রতিটি সৈন্যদলের থেকে উত্থিত হচ্ছে সেই গানের সুর।
সেই গানের সুর ক্রমশই এগিয়ে আসতে থাকে, উথিত হতে শুরু করে প্রতিটি সৈনিকের কণ্ঠ থেকে। এবং মৃত্যু যখন আমাদের দলের সর্বব্যাপী ধ্বংস করতে উদ্যত, তখনো আমরা পাশের লোকের উদ্দেশ্যে গেয়ে চলেছি : জার্মান, প্রিয় জার্মান দেশ আমরা সবচেয়ে ওপরে, পৃথিবীর সমস্ত দেশের ঊর্ধ্বে।
চারদিন যুদ্ধক্ষেত্রের একটা খানায় কাটিয়ে আমরা ফিরে আসি। এমন কি আমাদের পদক্ষেপও আর আগের মত দীর্ঘ পড়ে না। সতের বছর বয়স্ক বালকদের যেন পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ বলে মনে হয়। এ উল্লিখিত সৈন্যদের কারোরই সমরশিক্ষার পরিপূর্ণতা ছিল না। কিন্তু আমরা অভিজ্ঞ সৈন্যদের মত মরতে জানতাম।
এটা মাত্র আরম্ভ এবং এ জিনিসগুলোকেই আমরা বছরের পর বছর বহন করে নিয়ে। গেছি। ভাবপ্রবল যুদ্ধের উৎসাহের বদলে একটা তীব্র ভীতি তখন জড়িয়ে ধরেছে। উৎসাহ তারপর ধীরে ধীরে কমে আসে এবং আরম্ভের প্রচণ্ড রকমের উৎসাহটা নিভে গিয়ে সব সময় একটা মৃত্যুভয়ের ছায়া সর্বত্র দেখতে থাকি। এমন একটা সময় আসে, যখন পরস্পরের মধ্যে তর্ক বেঁধে যায় একটা প্রশ্ন নিয়ে, কর্তব্যের আহ্বান বড়, নাকি আত্মরক্ষা; এবং আমাকেও সেই তর্কের মধ্য দিয়েই চলতে হয়েছে। মৃত্যু তখন সর্বত্র তার প্রার্থনা জানিয়ে চলেছে, একটা নামহীন কাঠিন্য যাকে বলে বিদ্রোহত্মক মনোভাব দুর্বল শরীরে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং আপ্রাণ চেষ্টা করে সহজাত জ্ঞান বলে অভিহিত হতে। কিন্তু বাস্তবে এটা আর কিছুই নয় — ভয়; যা ব্যক্তিগতভাবে সকলকেই আক্রমণ করে বসেছিল। যত অধিক সংখ্যক কণ্ঠস্বরের পরিণামদর্শিতার কথা ভেবে নিজেদের মনোবল বাড়াবার কথা ভাবি, তত বেশি তার আবেদন নিবেদন স্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায়, প্রতিরোধ শক্তিও বেড়ে ওঠে। শেষে একসময় অন্তর্দ্বন্দ্ব শেষ হয় এবং কর্তব্যের আহ্বানে বিজয়ী হয়। ১৯১৫-১৬ সালের পুরো শীতটাই আমাকে এ সগ্রামের মধ্যে দিয়ে কাটাতে হয়েছে। ইচ্ছাশক্তি শেষমেষ প্রভুত্ব বিস্তার করে। প্রথমদিকে আমি এ সংগ্রাম হাসিমুখেই করেছি, বর্তমানে কিন্তু আমার মধ্যে এক শান্তভাব আর স্থির সংকল্প এসেছে এবং যা আমার মনের সহাশক্তির পরিধিও অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। ভাগ্য সম্ভবত এবার তার শেষ পরীক্ষায় হাজিরা দেওয়ার কথা বলতে শুরু করেছে, অবশ্যই আমার মানসিক দৃঢ়তা এবং যৌক্তিকতাকে বাদ দিয়ে। যুবক স্বেচ্ছাসেবকরা বর্তমানে অভিজ্ঞ সৈনিকে পরিণত হয়েছে।
এ একই ধরনের পরিবর্তন সমস্ত সৈন্যদলের মধ্যেই আসে। অবিরত সংগ্রাম এটাকে অভিজ্ঞ এবং শুধু দৃঢ়তা করেনি, শক্তও করেছিল; যার জন্য এটা দৃঢ় বদ্ধ এবং ভয়হীন চিত্তে তার প্রতিটি কার্যকলাপের সম্মুখীন হতে পেরেছে।
একমাত্র বর্তমানেই সেই সৈন্যদলকে বিচার করা সম্ভব। দু-তিন বছর ক্রমাগত সংঘর্ষের পর, এক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আরেক যুদ্ধক্ষেত্রে, উন্নত সৈন্যদল এবং অস্ত্রশস্ত্রের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে, অনাহার এবং ক্লান্তি ক্লেশের শেষ সীমায় পৌঁছে, সময় এসেছে যখন একজন সৈনিক তার ব্যক্তিগত সংঘর্ষের মূল্য বুঝতে সক্ষম।
আগামী এক হাজার বছরেও মহাযুদ্ধের জার্মান সৈন্যদের বীরত্ব তারা স্মরণে আনবে এবং তখন ধূসর অতীত থেকে জেগে ওঠা ওমর দৃষ্টি কখনই স্বীকার করবে না। যে এ শিরস্ত্রাণগুলো কখনো ভয়ে সংকুচিত হয়েছে বা স্পষ্টভাবে ভয়ে কথা বলেনি। যতদিন পর্যন্ত জার্মান জাতির অস্তিত্ব থাকবে, তারা এভাবে গর্ববোধ করবে যে এরা তাদের পূর্ব পুরুষের সন্তান।
আমি তখন ছিলাম, একজন সৈনিক, তাই অযথা রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিনি। এর আরো একটা কারণ হল সময়ও তখন ঠিক এর স্বপক্ষে ছিল না। আমি এখনো পর্যন্ত বিশ্বাস করি যে সাধারণ একটা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছেলে আজকের শ্রেষ্ঠসন্তানের চেয়েও অনেক বেশি দেশের সেবা করেছে। আমি অবশ্য শ্রেষ্ঠ সন্তান বলতে গণতান্ত্রিক সদস্যদের বোঝাতে চাইছি। সেইসব তুচ্ছ লোকগুলোর প্রতি আমার তীব্র ঘৃণার একমাত্র কারণ হল, সেই দিনগুলোয় ভাল লোকগুলোর যা বলার থাকত তা শত্রুর মুখের ওপরেই বলত এবং তা বলতে অপারগ থাকলে মুখ বন্ধ করে তাদের কর্তব্য অন্য কিছুতে নিয়োজিত করত। আমি এ রাজনৈতিক বিশারদদের মনে মনে ঘৃণা করতাম এবং আমার যদি কোন উপায় থাকত তবে আমি তাদের নিয়ে একটা শ্রমিক দল তৈরি করতাম যা নাকি তাদের নিজেদের ভেতরের টগবগে সুযোগের প্রতীক্ষাটাকে প্রস্ফুটিত হতে সাহায্য করে তাদের হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে দিত; সৎ এবং ভাল মানুষেরা তাহলে এদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হত না।
সেইদিনগুলোয় আমি রাজনীতিকে কোনরকম গুরুত্ব দিতাম না। কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু অভিব্যক্তির ব্যাপারে আমার মতামত প্রকাশ না করে পারিনি, যা শুধু জাতির স্বার্থেই আঘাত হানেনি, তা’ বিশেষ করে সৈনিকদের স্বার্থেরও পরিপন্থী। এর মধ্যে দুটো বিষয়ে আমার প্রচণ্ড রকমের উদ্বিগ্নতা ছিল, যা আমার ধারণায় আমাদের স্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকারক।
আমাদের প্রথম পরপর বিজয়গুলির অব্যহত পরেই সংবাদপত্রের একটা বিশেষ গোষ্ঠী জনসাধারণের উৎসাহের আগুনে ফোঁটা ফোঁটা ঠাণ্ডা জল ফেলতে থাকে। প্রথমদিকে বেশি লোকের নজরে ব্যাপারটা আসেনি। সৎ উদ্দেশ্যের ছদ্মবেশে এবং নকল উদ্বিগ্নতার ভাণ দেখিয়েই করা হয়েছে। জনসাধারণকে বোঝানো হয়েছে যে জয়ের বিরাট জয়োৎসব ঠিক এ জায়গাতে সমীচীন নয়। আর শ্রেষ্ঠ একটা জাতির পক্ষে এটা সাজে না। জার্মান সৈনিকের সহিষ্ণুতা এবং শৌর্য হল মেনে নেওয়া সত্য, যার জন্য জয়োৎসবের এ সশব্দে বিদিরণের কোন প্রয়োজনীয়তাও নেই। উপরন্তু, বিদেশীরা জয়ের এ অভিব্যক্তিকে কিভাবে নেবে? এ জান্তব জয়োল্লাসের চেয়ে শান্ত এবং দ্ৰ উপায়ে জয়ের বহিঃপ্রকাশকে কি তারা আরো ভালভাবে গ্রহণ করবে না। সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রগুলো এ কথাও প্রচারিত করতে শুরু করে যে, জার্মানদের উচিত স্মরণে রাখা যে যুদ্ধ আমাদের কাজ নয়, সুতরাং জাতিকে ডেকে তাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নেওয়াটা আমাদের পক্ষে কিছু লজ্জাস্কর নয়। এ কারণেই আমাদের সৈনিকদের এ সমুজ্জ্বল কাজকে কোনরকমেই অশোভনীয় বিজয়োৎসবের মাধ্যমে কলংকিত করাটা উচিত হবে না। কারণ বহিঃপৃথিবী কিছুতেই ব্যাপারটাকে বুঝে উঠতে পারবে না। উপরন্তু, সত্যিকারের একজন নায়ক নিশুপ বিনয়ের সঙ্গে তার কাজ করে এবং ভুলেও যায়, এর চেয়ে বড় সার্থকতা আর কিসে! মোটামুটি এ ছিল তাদের সতর্কতার উপসংহার।
এসব লোকগুলোর কান ধরে খামচে টেনে এন গলারদড়ির ফাঁস পরানোর পরিবর্তে, যাতে জাতির এ বিজয়োৎসবে ভাটা না পড়ে, এ সমস্ত তথাকথিত নাইটদের কলমকে তুলে ধরাই হয়েছিল, যা ক্রমাগত এ বিজয়োৎসবকে ‘অশোভনীয় এবং মর্যাদাহানিকর বলে চিৎকার করেছে।
সম্ভবতএকজনেরও এ ধারণা ছিল না যে একবার যদি গুণ উৎসাহ কোনরকমে নিভে যায়, তবে তাকে আর কোনক্রমেই আবার প্রজ্জ্বলিত করা সম্ভব নয়, যখন প্রয়োজন পড়বে।
এ উৎসাহও এক প্রকারের সুরামত্ততা এবং তা সযত্নে রাখা উচিত। এ ধরনের উদ্যমের অভাবে কি করে এতবড় একটা যুদ্ধকে সহ্য করা সম্ভব, যা নাকি মনুষ্যত্বের পরিমাপে একটা জাতির পক্ষে বিরাট অক্লান্ত পরিশ্রম করার চাহিদার অপেক্ষা রাখে।
বিশাল জনতার মনস্তত্ত্ব আমি খুব ভালভাবেই বুঝতে পারতাম এবং জানতাম এসব ক্ষেত্রে মহান রুচিজ্ঞান আগুনকে বাতাসের সাহায্যে বাড়িয়ে তুলে লোহাকে গরম রাখতে সমর্থ হবে না। আমার কাছে এটা ভুল যে জনসাধারণের উৎসাহটাকে আরো উঁচু গ্রাম তুলে ধরা হয়নি।
সুতরাং আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না, কেন এ ধরনের নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। অর্থাৎ জনসাধারণের উৎসাহকে ভিজিয়ে দেওয়ার নীতি।
আরেকটা ব্যাপার যা আমাকে অসহিষ্ণু করে তুলেছিল, তা হল মার্কসীয় মতবাদকে যেভাবে গ্রহণ এবং শ্রদ্ধা করা হয়েছিল, আমি ভেবেছিলাম এর কারণ হল মার্কসীয় প্লেগ সম্পর্কে এদের ধারণা ছিল কত অল্প। সবাই বিশ্বাস করত যে দলীয় মতপার্থক্য যুদ্ধের সময়ে দূর করার প্রচেষ্টাই মার্কসীজিমকে এত নরম আর উদার হিসেবে জনসাধারণের কাছে প্রতিফলিত করেছিল।
কিন্তু এখানে তো দলের কোন প্রশ্নই নেই। এখানে হল সেই মতবাদের প্রশ্ন যা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল শুধুমাত্র একটা উদ্দেশ্য নিয়ে অর্থাৎ মানবজাতিকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিতে। এ মতবাদের অভিপ্রায়টাকে কেউ বুঝতে পারেনি কারণ আমাদের ইহুদী দলিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এ প্রশ্ন কখনো উত্থাপন করেনি; এবং আমাদের উদ্ধত আমলা অফিসাররা বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট তালিকার বাইরের কিছু পড়াশুনা করতে রাজী নয়। তাই এ শক্তিশালী বিদ্রোহের স্রোত তাদের পাশ কাটিয়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু যারা বুদ্ধিমান বলে সমাজে পরিগণিত,–তারা কখনো প্রসন্ন দৃষ্টিতে এদিকটায় নজর দেয়নি। এ কারণেই রাষ্ট্রীয় সংগঠন সবসময়েই ব্যক্তিগত মালিকানার সংগঠনের পেছনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে। এ ভদ্রসম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে একথাই বলা চলে যে, তাদের মতামত হল : যা আমরা জানি না,–তা নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজনও নেই। ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে জার্মান শ্রমিকেরা মার্কসবাদের ধার ঘেঁষে দাঁড়ায়। এটাই হল বিরাট একটা ভুল। যখন সেই দুর্গের মুহূর্তগুলো এসে উপস্থিত হয়, তখন প্লেগের কবলে পড়ে জার্মান শ্রমিকেরা নড়ে ওঠে। নইলে সগ্রামের জন্য না ছিল তারা ইচ্ছুক, না ছিল তাদের প্রস্তুতি। এবং জনসাধারণের মুখামীও যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল যে কারণে তারা মাকর্সবাদ জাতীয় নীতি বলে কল্পনা করত। এটা হল আরো একটু উপযুক্ত উদাহরণ অর্থাৎ যারা তাত্ত্বিক তারা মার্কসবাদ শিক্ষার প্রচলিত ধারাটাকে খতিয়ে দেখেনি। যদি তারা খতিয়ে দেখত, তবে এ ধরনের ভুল কিছুতেই হওয়া সম্ভব ছিল না।
মার্কসবাদ, যার মূল উদ্দেশ্যই ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে সমস্ত অ-ইহুদী রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা। ১৯১৪ সালে এটা প্রত্যক্ষ হয় যে কিভাবে জার্মান শ্রমিকবৃন্দকে উঁচু গলায় তিরস্কার করা হয়েছে, যা জাতীয় উৎসাহের থেকে উৎসাহিত হয়ে পিতৃভূমির সঙ্গে মিশে গেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই সেই শঠতাপূর্ণ ধোয়ার পর্দা কুখ্যাত জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার হাল্কা হাওয়ায় মিলিয়ে আসে, এবং হঠাৎ ইহুদী পদস্থ ব্যক্তিরা তাদের নিঃসঙ্গ এবং পরিত্যক্ত বোধ করে। সেই মুর্থ এবং পাগলের কোনরকম পদচিহ্ন রেখে যায়নি; যা গত ষাট বছর ধরে জার্মানদের শরীরে রোগের বীজ ছড়িয়ে আসছে। সত্যি কথা বলতে গেলে, জার্মান শ্রমিকদের পক্ষে এটা অত্যন্ত অমঙ্গল সূচক ছিল। যে মুহূর্তে নেতারা উপলব্ধি করতে পারে যে বিপদ সামনে উপস্থিত যা তাদের টেনে নিচে নামাবে, তারা প্রবঞ্চনার টুপিটা তাদের কানের ওপর টেনে তুলে দেয় যাতে তাদের কেউ চিনতে না পারে। তারা প্রকৃত ঘটনার প্রদর্শনকারী প্রহসনের অভিনেতার ভূমিকা গ্রহণ করে যেন। জাতিয় অভ্যুত্থানের প্রধান দায়িত্ব তাদের ওপরেই ন্যস্ত।
আমার মনে হয় জনসাধারণের আপদ ইহুদী দলের বিরুদ্ধে যথাযোগ্য কাজ শুরু করার সময় এসে গেছে। যে কোনরকম ফলাফলের মুখোমুখি তৈরি রেখেই ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। তাতে জনসাধারণের ভাগ্য কাটাগাছের ঝোপে ভর্তি জঙ্গলেই পড়ুক বা প্রতিবাদই করুক। আগস্ট ১৮১৪ সালের এক ধাক্কায় শূন্যগর্ভ ইতরগুলো আন্তর্জাতিক সমস্বার্থতায় জার্মান শ্রমিকদের মাথাগুলোকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, কয়েক সপ্তাহ পরে,–নিজেদের কানে এ নির্বুদ্ধিতার কথা শোনার পরিবর্তে। আমেরিকর তৈরি, বোমাগোলার আওয়াজে কান ঝালাপালা হবার জোগাড়, মাথার ওপরে মুমুর্থ ফাটা এসব বোমাগোলাকে আন্তর্জাতিক সহকর্মী প্রীতির প্রতীক বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে সেই জার্মান শ্রমিকেরা জাতির জন্য রাস্তা আবার আবিষ্কার করেছে, যে কোন সরকারের এটা কর্তব্য–অবশ্যই যে সরকার তাদের লোকদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, — এ সুযোগে এসবের নির্দয়ভাবে মুলোৎপাটন করা, যা কিছু জাতির উৎসাহকে অবদমিত করার চেষ্টা করবে।
সুতরাং বিষাক্ত এ সাপেরা আবার তাদের কাজ শুরু করে। এবার অবশ্য আগের চেয়ে আরো বেশি সতর্ক হয়ে, তবে আরো ধ্বংসাত্মক উপায়ে। যখন সৎ লোকেরা বন্ধুত্ব পুনঃস্থাপনের প্রচেষ্টায় রত, ঠিক সেই মুহূর্তে মিথ্যা শপথকারী এসব অপরাধীরা একটা বিদ্রোহের জন্য তৈরি হচ্ছে।
স্বভাবতই আমার মনে তখন দ্বিধা, কোন পথটাকে ঠিক সেই সময়ে বেছে নেওয়া উচিত; কিন্তু এর ফলাফলের যে এতটা ধ্বংসাত্মক হবে তা ভাবিনি।
তবে তাহলে তখন কি করা উচিত? এ সম্ভব চক্রের নেতাদের ধরে চালান দিয়ে জেলে পুরে জাতিকে এদের হাত থেকে মুক্ত করা? সামরিক ব্যবস্থার সাহায্যে এদের একেবারে নির্মূল করে দেওয়া উচিত ছিল। দলবাজী বিলুপ্ত এবং পার্লামেন্টকে প্রয়োজনে বন্দুকের নলের সামনে ধরে তার জ্ঞানবুদ্ধ ফিরিয়ে আনা উচিত ছিল। এর চেয়ে আরো ভাল ব্যবস্থা হত যদি পার্লামেন্টকে ভেঙ্গে দেওয়া হত। এখন যেমন গণতন্ত্র যে কোনও দলকে ইচ্ছে মত ভেঙে দেয়। কিন্তু সে দিনগুলোতে এ কাজের প্রয়োজনীয়তা আরো বেশি ছিল। কারণ জাতির অস্তিত্বই তখন চরমভাবে বিপন্ন। অবশ্য এ ধরনের উপদেশ একটা প্রশ্ন তুলতে বাধ্য : যন্ত্রের সাহায্যে কি আদর্শের মূলোৎপাটন করা সম্ভব? সার্বজনীন একটা মতবাদকে কি গায়ের জোরে আক্রমণ করা যায়?
সেই সময় এ প্রশ্নটাকে আমি আমার নিজের মনে বার বার জিজ্ঞাসা করেছি। একই ধরনের সমস্যাকে বিশ্লেষণ করে, ইতিহাস থেকে তার নজীর নিয়ে, বিশেষ করে ধর্মের থেকে যাদের উৎপত্তি, আমি নিচের মতামতগুলোয় উপস্থিত হই।
আদর্শ, দার্শনিক মতবাদ এবং কোন সংগ্রাম যার ভিত্ ধর্মের মাটিতে প্রোথিত, সত্যি মিথ্যে যা-ই হোক না কেন, শক্তি দ্বারা তার মূলচ্ছেদ করা একটা নির্দিষ্ট অবস্থার পর সম্ভব নয়, একমাত্র একটা পদ্ধতিতেই তা সম্ভব সেটা হল : এ শক্তি যদি কোন নতুন আদর্শ বা মতবাদের জননকেন্দ্রকে নির্দয়ভাবে নির্মূল করা যায়, এমন কি সেই আদর্শের ধ্বজা ধরে থাকা শেষ মানুষটা অথবা সেই আদশের প্রচলিত ধারাটাকে মুছে দিতে হবে, নইলে তা সব সময়েই চেষ্টা করবে, পেছনে একটা ধারা রেখে যাওয়ার। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এর ফলাফল হল রাষ্ট্রকে বর্জন করা, তা সাময়িক বা চিরস্থায়ী হোক, রাষ্ট্রের সৌজন্যের পেছনে রাজনৈতিক রহস্য থাকে। কিন্তু অভিজ্ঞতা আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে যে এ সমূলোৎপাটন রক্তস্রাবী পদ্ধতিতে কিছু ভাল লোককে এ নির্যাতিত শাসনব্যবস্থায় নিগৃহীত হতে হয়। সত্যি বলতে কি প্রতিটি নির্যাতন যার পেছনে কোন প্রেরণা নেই, তা নীতির দিক থেকে অন্যায় এবং তার দ্বারা কিছুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ মানব সন্তানকে আমরা হারাই, এর পরিমাণ সময় সময় এতই বেশি হয়ে দাঁড়ায় যে নির্যাতনটাকে অন্যায় বলে মনে হয়। অনেক ব্যক্তির কাছেই এটা নিছক বিরুদ্ধপক্ষকে দমন করার প্রবণতা, প্রতিটি ব্যাপারেই তারা চেষ্টা করে নির্দয়ভাবে শক্তির দ্বারা বিনাশ করতে।
এভাবে নির্যাতন যত বেড়ে চলে, নির্যাতনের মতবাদটাও তত বৃদ্ধি পায়। নতুন মতবাদের মাধ্যমে এ ব্যবস্থার বিনাশ সম্ভব। কিন্তু এ ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এ পদ্ধতির জন্য আমরা জাতির বা রাষ্ট্রের কিছু সংখ্যক শ্রেষ্ঠ সন্তানকে হারাব এবং সে রক্তও তখন প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হবে, কারণ এ ধরনের আংশিক বা সামগ্রিক পরিষ্কার করার কাজে জাতির শক্তি নিঃশেষের মুখোমুখি এসে দাঁড়াবে। এ ধরনের নীতি সব সময়ই নিরর্থকতায় পর্যবসিত হয় যদি শুরু থেকে এ মতবাদ ছোট্ট গণ্ডীর বাইরে ছড়িয়ে পড়ে।
এসব কারণে এসব ক্ষেত্রৈ অন্যান্য বুদ্ধির মত এ মতবাদকে ভূমিষ্ঠ অবস্থাতেই নির্মূল করা সম্ভব। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এর প্রতিরোধ ক্ষমতাও বেড়ে চলে। বয়সের সঙ্গে এর ভেতরে ঠাঁই নেয় নব্য যুবকেরা–তবে অন্যরূপে এবং অন্য উদ্দেশ্য নিয়ে।
সুতরাং এ সত্য প্রতিষ্ঠিত যে কোন মতবাদকে নির্মূল করার প্রচেষ্টা, যদি সে প্রচেষ্টার ধর্মীয় কোন ভিত্তিভূমি না থাকে এবং শুধু মতবাদই নয়, — সে ধরনের দল বা পার্টিকে যা এসব মতবাদের দ্বারা সৃষ্ট, অনেক ক্ষেত্রেই উল্টো ফল প্রাপ্তি যোগ ঘটে থাকে। এবং সেগুলো হয় নিচের কারণে?
সে মতবাদ বিস্তারের মুখোমুখি যখন নিছক শক্তির প্রয়োগ হয়, তখন সে শক্তি প্রয়োগ ক্রমাগত এবং একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে হওয়া উচিত। এর মানে গিয়ে দাঁড়ায়, কোন মতবাদকে নিশ্চিহ্ন করতে হলে ক্রমাগত এবং সমানুপাতিক কোন পদ্ধতির প্রয়োজন। সেই মুহূর্তে দ্বিধা দেখা দেবে, এবং সহ্য ক্ষমতার হেরফেরের জন্য শক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে শুধুমাত্র সেই মতবাদই যে প্রখর হয়ে উঠবে, তা’ নয়, কিন্তু প্রতিটি নির্যাতন নতুন নতুন সমর্থক জোটাবে যারা এ পদ্ধতিতে নির্যাতিত। পুরনো কর্মীরা আরো তিক্ত হয়ে উঠবে যার দ্বারা এ পদ্ধতিতে নির্যাতিত এবং তাদের মৈত্রীবৃন্দো আরো বেশি শক্তি বৃদ্ধি পাবে। তাই শক্তি যখন প্রয়োগ করা হয়, সাফল্য নির্ভর করে সেই শক্তির ভারসাম্যতার ওপরে। এ অধ্যাবসায় হল আর কিছুই নয়, নির্দিষ্ট ধর্মীয় মতবাদ। শক্তির প্রতিটি রূপ যার পেছনে ধর্মের দোহাই থাকে না, তা এলোমেলো এবং অনির্দিষ্ট হতে বাধ্য। এ ধরনের শক্তির ক্ষেত্রে দেখা যাবে স্থিরতার অভাব, একমাত্র বিশ্বজনীন মতবাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যা শ্রেষ্ঠতম হওয়ার পথে চলেছে। ব্যক্তিগত উৎসাহের বহিঃপ্রকাশ হল এ ধরনের শক্তি; সুতরাং সময়ের এবং মানুষের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যার হাতে এর ভার পড়েছে তার চরিত্র এবং ব্যক্তিগত ক্ষমতার পরিপ্রেক্ষিতে এরও পরিবর্তন ঘটে থাকে।
কিন্তু এটার সম্পর্কে আরো কিছু বলার আছে। প্রতিটি বিশ্বজনীন মতবাদ,–ধর্মীয় বা রাজনৈতিক যা-ই হোক না কেন–অনেক সময়েই আরম্ভ বা শেষ কোথায় তা ধরা। মুস্কিল হয়ে পড়ে, বিরুদ্ধে মতবাদের নেতিবাচক আদর্শের জন্য যত না সংঘর্ষ লাগে, তার চেয়ে অনেক বেশি হয় তার নিজস্ব আদর্শের ইতিবাচক ধ্যান ধারণার কারণে। এ সংঘর্ষের মূল কারণ হল আক্রমণে আত্মরক্ষণে নয়। আর একটা সুবিধে হল এর বস্তুতান্ত্রিকটা কোথায় তা বোঝা যায়, কারণ এ বস্তৃতান্ত্রিকতাই হল এর নিজস্ব আদর্শ। বিপরীতভাবে এটা বলা দুস্কর কখন নেতিবাচক উদ্দেশ্য বিরুদ্ধপক্ষের মতবাদকে ধ্বংস করতে অগ্রসর হবে এবং কার্য সম্পাদন করবে। এ একমাত্র কারণে বিশ্বজনীন মতবাদ হল চরিত্রের দিক থেকে আক্রমণাত্মক, যার ছক নির্দিষ্ট এবং প্রচণ্ড শক্তিশালী ও চরিত্রগতভাবে স্থির; বিশেষ করে যে সর্বজনীন মতবাদ আত্মরক্ষার কারণে বেছে নেওয়া হয়। সেই শক্তি আত্মরক্ষণের জন্যই ব্যবহৃত হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না এর ব্যবহারকারীরা উপযুক্ত এবং নতুন ধর্মীয় মতবাদের প্রচারক বলে প্রতিপন্ন হচ্ছে।
সংক্ষেপে নিচের ব্যাপারগুলোকে মনে রাখতে হবে : সর্বজনীন মতবাদের বিরুদ্ধে শক্তি নিয়োজিত প্রতিটি যুদ্ধ নিষ্ফলতায় পরিবেশিত হবে, যদি সেই সংঘর্ষ আত্মরক্ষণ ধরনের এবং নতুন কোন ধর্মীয় মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হয়। একমাত্র বিশ্বজনীন দু’টো মতবাদের ভেতরে দৈহিক শক্তি ক্রমাগত এবং নির্দয়তার সঙ্গে সম্পাদন করা যায়, যা শেষপর্যন্ত নিজের দিকের পাল্লা ভারী করবে। মার্কসবাদের সংঘর্ষে পরাজয়ের কারণ এখানেই।
এ কারণেই বিসমার্কের সমাজ বিরুদ্ধ আইন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, এবং যা ভবিষ্যতেও ব্যর্থ হতে বাধ্য। নতুন কোন সার্বজনীন মতবাদের ভিতই ছিল না যার উন্নতির ও অগ্রসরতার দরুন এ সংঘর্ষকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। বলা যেতে পারে শাসকবৃন্দ বা আইনকানুন বজায় রাখার জন্য পর্যাপ্ত শাসনব্যবস্থার ভিত্তিভূমি যার থেকে জীবন মৃত্যুর যুদ্ধের শক্তি আহরণ করা সম্ভব। যা একমাত্র উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী পণ্ডিত মূর্বদের চিৎকারেই প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।
এর প্রধান কারণ হল, এর পেছনে পর্যাপ্ত পরিমাণে ধর্মীয় কারণ ছিল না যার জন্য বিসমার্ক ব্যর্থ হয়েছিলেন তার সামাজিক আইনগুলোর বিচার এবং মেনে নেওয়ার জন্য এমন কোন গোষ্ঠীর কাছে যারা নিজেরাই মার্কসবাদের ফল বিশেষ। এভাবে সেই লৌহ সম্রাট যখন তার নিজের ভাগ্যকে মার্কর্সতত্ত্বের মধ্যবিত্তশ্রেণীর গণতন্ত্রের দিকে চালনা করে, তখন পুরো ব্যাপারটাই একটা হাস্যকর পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়। সে বাগানের পরিচর্যার জন্য তার উদ্দেশ্য থেকে সরে আসে। কিন্তু এটা হল সার্বজনীন মতবাদের বিফলতার কারণ যা একদা মানুষকে আকর্ষণ করেছিল এবং যে ভিত্তিভূমি থেকে তাকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। এভাবে বিসমার্কের প্রচার পদ্ধতির ফলাফলটা সত্যই বিলাপের কারণ।
যতই আমি তকালীন সরকারের সোশ্যাল ডেমোক্রাসির প্রতি মনোভাব পবির্তনের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করি, ঠিক যা মার্কসবাদের বিরুদ্ধে সমিতিবদ্ধ হবে, ততই আমি বেশি করে উপলব্ধি করি যে এ মতবাদের বদলে বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে কোন মতবাদ থাকা উচিত। যদি সোশ্যাল ডেমোক্রাসিকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়, তবে তার পরিবর্তে জনসাধারণকে কি উপহার দেওয়া হবে? এমন একটা আন্দোলনের অস্তিত্ব বর্তমানে নেই যা বিরাট এ কর্মীদলকে আকর্ষণ করতে পারে। এদের অবস্থা নেতৃত্ব ছাড়া যে
নেতৃত্বের অপেক্ষায় এ কর্মীদল অপেক্ষারত। এটা একটা বোকার মত কল্পনা যে আন্তর্জাতিক গোড়ার দল যারা এতদিন ধরে শ্রেণী সংগ্রামে যুক্ত, অবিলম্বে তারা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সঙ্গে হাত মিলাবে, অথবা আরো একটা শ্রেণী সংঘ গড়বে। এ সংঘগুলোকে আপাতদৃষ্টিতে যতই অসন্তোষের চোখে দেখা হোক— একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, এ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক নেতারা এ শ্রেণীর পার্থক্যকে সামাজিক জীবনের একটা প্রধান অঙ্গ বলে পরিগণিত হত, যদি এটা রাজনৈতিক দিক থেকে তাদের অসুবিধার সৃষ্টি করত। এ সত্যকে যদি তারা অস্বীকার করে, তবে তারা শুধু অপরিণামদর্শীই নয়, মিথ্যাভাষণেও পটু বটে।
বিশেষভাবে বলতে হয়, সবার বোঝা উচিত যে জনসাধারণকে তারা যতটা বোকা মনে করে, সত্যিকারের তারা ততটা বোকা নয়–এ সত্যটাকে রক্ষা করা। রাজনৈতিক ব্যাপারে এটা প্রায়ই মনে হয়ে থাকে যে অনুভব শক্তি জনসাধারণের বুদ্ধিমত্তার চেয়ে অনেক প্রখর। যদিও মতামতের দিক থেকে বলা হয়ে থাকে যে অনুভূতি শক্তির জন্যই আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ওরা এত বোকা–এ যুক্তি খণ্ডানো যায় যদি আমরা এ সত্যটাকে বিবেচনা করি যে শান্তিবাদী গণতন্ত্রও কম দুর্বল নয়। যদিও এরা সমস্ত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের থেকে সমর্থক আহরণ করে থাকে, যতদিন পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ নাগরিক সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির সংবাদপত্র যা বলছে তা গোগ্রাসে গিলবে।
সবারই সতর্কভাবে এ বিপরীত সত্যকে বিচার বিশ্লেষণ করা উচিত। এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে এ শ্রেণী সংগ্রামের সঙ্গে আদর্শের কোন সম্পর্ক নেই, যদিও নির্বাচনের সময়ে এ মাদকতাই ওষুধ হিসেবে কাজ করে। আমাদের এ বিশাল জনতা এ শ্রেণী বিষয়ে ভীষণ জেদী। এটা কাব্যের দিবাস্বপ্ন দেখা নয়, এ হল সত্যিকারের বাস্তব অবস্থা। এ মনোবৃত্তি শুধু আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিমান শ্রেণীর মানসিক ধারার পরিচয়ই বহন করে না। এটাও প্রমাণ করে তারা যে পরিবেশে মার্কস নামক প্লেগটা বেড়ে চলেছে তা অনুধাবন করতেও অক্ষম; কারণ মার্কসতত্ত্ব আমরা যা হারিয়েছি তা পুনরুদ্ধার করতে কখনই সক্ষম হবে না।
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সংগঠন–এ নামে যারা নিজেদের পরিচিতি দিয়েছে–কখনই নিম্নশ্রেণীর ওপরে তাদের প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না বা তাদের ধারণাটাকে বদলাতে পারবে না। তার কারণ দুটো পৃথিবী ঠিক বিপরীতভাবে দুই মেরুতে দাঁড়িয়ে। এর একটা অংশ প্রাকৃতিক আর অপর অংশ কৃত্রিম উপায়ে দ্বি-খণ্ডিত। এ দুই পক্ষেরই কিন্তু চিন্তাধারা এক, এবং সেটা হল পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের সংঘর্ষ। কিন্তু এ ধরনের সংঘর্ষে নবীনরাই জয়ী হবে, অর্থাৎ মার্কসবাদ।
১৯১৪ সালে সোশ্যাল ডেমোক্রাসির বিরুদ্ধে সংঘর্ষটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল। কিন্তু বাস্তবে কোন পরিবর্তনের জন্য কবে এ সংঘর্ষ শেষ হবে, তা নিয়ে দ্বিধা দেখা দেয়। সে জায়গায় জেগে উঠে একটা শূন্যতা।
যুদ্ধের অনেক আগেই আমার ধারণা ছিল, যে কারণে তঙ্কালীন কোন রাজনৈতিক দলেই যোগ দেইনি। যুদ্ধের সময়ে আমার এ মনোভাব আরও দৃঢ় হয় যে সচরাচর পথে সোশ্যাল ডেমোক্রাসির বিরুদ্ধাচারণ অসম্ভব; কারণ তার জন্য এ রকম একটা দলের প্রয়োজন যা শুধু সংসদীয় দল নয়, তার চেয়ে কিছু বেশি। কিন্তু সেরকম কোন দল তখন ছিল না।
আমার অন্তরঙ্গ সহকর্মীদের সঙ্গে এ ব্যাপারটা নিয়ে আমি প্রায়ই আলোচনায় বসতাম। এবং এ সময়েই আমি স্থির প্রত্যয় হই যে ভবিষ্যত জীবনে আমাকে রাজনীতির আসরে ঢুকতে হবে। আমি মাঝে মাঝেই বন্ধুদের যা প্রতিশ্রুতি দিতাম সেটাই আমাকে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করে যুদ্ধের পরে। অবশ্যই আমার পেশাগত কাজের পাশাপাশি। এবং এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে এ পথ আমি অনেক চিন্তা-ভাবনার পরেই বেছে নিয়েছিলাম।
০৬. যুদ্ধের প্রচারকার্য
রাজনৈতিক ঘটনাবলীর গতিপথ নীরিক্ষণ করতে গিয়ে আমাকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ করত এর সংঘবদ্ধ প্রচারকার্যের সজীব দিকটা। মার্কসবাদীরা খুব ভালভাবেই জানত এ যন্ত্র কী করে বাজাতে হয়, এবং বাস্তবক্ষেত্রে তার সঠিক প্রয়োগ। শীঘ্র আমি উপলব্ধি করি যে, সঠিক সংঘবদ্ধ প্রচারকার্যটা শিল্পের পর্যায়ে পড়ে এবং এ শিল্প আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কাছে একেবার অজানা। লুইগারের সময়ে খ্রিস্টান–সোশ্যালিস্ট পার্টি একমাত্র এ যন্ত্রের কিছুটা প্রয়োগ করে, এবং তাদের সাফল্যের জন্য তারা যথেষ্ট পরিমাণে এর কাছে ঋণী।
যুদ্ধের সময়েই একমাত্র আমরা বুঝতে পারি যে সংঘবদ্ধ প্রচারকার্য নির্দিষ্ট নীতিতে চালিয়ে গেলে তাতে কী প্রচণ্ড সাফল্য আসে। কিন্তু এবারও দুর্ভাগ্যবশত ব্যাপারটাকে অন্যদিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়, আমাদের দিকের প্রচারকার্য যেভাবে করা উচিত ছিল–বাস্তবে করা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক নিকৃষ্টভাবে। জার্মান খবরাখবর পদ্ধতি এবারেও পরিপূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল–যে কারণে প্রতিটি সৈনিক ব্যর্থ হতে বাধ্য–এবং সেটাই আমাকে সংঘবদ্ধ প্রচারকার্য চালাবার ব্যবস্থার সমস্যা সম্পর্কে ব্যাপকভাবে আগ্রহী করে তোলে। আমার এ বিষয়ে বাস্তব শিক্ষা নেওয়ার প্রচুর সুযোগও ছিল। যদিও দুর্ভাগ্যবশত সেই শিক্ষা খুব ভাল মত দিয়েছিল আমাদের শত্রুরা। আমাদের দিকের দুর্বল দিকটা শত্রুরা খুব ভালভাবে ব্যবহার করেছিল এবং সেই ব্যবহারটা এত সার্থকভাবে রূপায়িত যে, যে কেউ অন্তত এ ব্যাপারে তাদের প্রচণ্ড রকমের প্রতিভাধর বলে স্বীকার করতে দ্বিধা করবে না। শত্রুদের সেই প্রচারকার্যের থেকেই আমি প্রশংসনীয়ভাবে আমাদের করণীয় কাজকে খুঁজে পাই। এর থেকে যে শিক্ষা নেওয়ার প্রয়োজন,–দুর্ভাগ্যবশত আমাদের পক্ষের তথাকথিত প্রতিভাধরদের সেদিকে কোন আকর্ষণই করেনি। তারা হল এ সবের উর্দ্ধে এসব শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে অনেক বেশি ধূর্ত। যাহোক, তাদের এ শিক্ষার কোন সৎ উদ্দেশ্যই ছিল না।
আমাদের তরফে কি কোনরকম সংঘবদ্ধ প্রচার কার্যের ব্যবস্থা ছিল? দুঃখের সঙ্গে তার উত্তরটা হল নেতিবাচক। এবং যা কিছু এ উদ্দেশ্যে করা হয়েছে, তা এতই অপ্রতুল এবং ভুলে ভরা যে তা প্রয়োজন মেটাবার পরিবর্তে ক্ষতিই করেছে বেশি। সংক্ষেপে পুরো ব্যবস্থাটাই ছিল অপ্রতুল। মনস্তত্বের দিক থেকেও সমস্ত ব্যাপারটাই ভুলে ভর্তি। যারাই মনোযোগের সঙ্গে জার্মান প্রচার কার্যের ব্যবস্থাটাকে অনুধাবন করেছে, তাদের বিচারে এ মতামত প্রকাশ পেয়েছে, আমাদের জনসাধারণের এমন কি এটার মূল প্রশ্নেও পরিষ্কার কোন ধারণা ছিল না।
প্রচারকার্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ও বটে। এর সম্পর্কে শেষের বিন্দুর মূল্যায়ণ ধরে এবং কি উদ্দেশ্যে এটা করা হচ্ছে–সেই উদ্দেশ্যটা সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণাও থাকা চাই।
এটাকে এভাবে সংঘবদ্ধ করতে হবে, যাতে এর নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে উপনীত হতে তা সাহায্য করবে, এবং একথা স্বীকৃত যে এর উদ্দেশ্য অনুসারে এর কর্মপদ্ধতিরও পরিবর্তন হয়ে যাবে। এবং প্রচারকার্যের চরিত্রও সে ভাবেই গঠিত হওয়া উচিত।
যুদ্ধের সময়ে আমরা যে কারণের জন্য লড়াই করেছিলাম তা যে শুধু মহত্ব ছিল তাই নয়, মানুষ যে কারণে কার্যশক্তি প্রয়োগ করতে পারে, সে কারণের জন্যই আমরা যুদ্ধ করেছিলাম। আমরা যুদ্ধ করেছিলাম আমাদের দেশের স্বাধীনতা এবং মুক্তির জন্য; আমাদের ভবিষ্যত মঙ্গলের এবং নিরাপত্তার খাতিরে, জাতির সম্মানের জন্য–বিতর্কমূলক সমস্ত মতামত সত্ত্বেও। একথা অনস্বীকার্য যে এ সম্মানের অস্তিত্ব বাস্তবে ছিল
, যার অস্তিত্বের প্রয়োজন অনস্বীকার্য যে জাতির সম্মান নেই, আজ হোক কাল হোক সে তার স্বাধীনতা এবং মুক্তি হারাবেই। এ ব্যাপারটা ঘটে উচ্চ বিচারকমের পদ্ধতির পথ ধরে, কাপুরুষের দলের স্বাধীনতার কোন দাবি-ই নেই। যে দাস, তার আবার সম্মান কিসের। সে সম্মানের উল্লেখটাই তার পক্ষে পরিহাসের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।
জার্মানি যুদ্ধে নেমেছিল তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। সুতরাং যুদ্ধের প্রচারকার্যের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ছিল যাতে যুদ্ধ করার উৎসাহটাকে বর্ধিত করা এবং সে যুদ্ধে জয়ের পথ প্রশস্ত করা যায়।
কিন্তু যখন জাতিরা তাদের অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজনে সংগ্রামে রত,–যখন অস্তিত্ব থাকবে কি থাকবে না, এ প্রশ্নের উত্তর অপেক্ষা করছে,–তখন সব রকমের মনুষ্যত্ব এবং রুচি ইত্যাদি বিষয়গুলো একপাশে সরিয়ে রেখে দেওয়াই যুক্তি সংগত। কারণ এসব আদর্শের অস্তিত্ব মানুষের সৃজনশীল চিন্তায় যা তার সঙ্গে সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। প্রকৃতি তাদের খোঁজও রাখে না। উপরন্তু খুব কম বা অল্প সংখ্যক জাতির এ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকে। মানবতা এবং রুচি বিজ্ঞান বিষয়ক আদর্শগুলো পৃথিবীর জনবসতির সঙ্গে অদৃশ্য হয়ে যাবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই জাতিও বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যারা এর সৃষ্টিকর্তা এবং রক্ষক।
যখন জাতি তার অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামে রত, তখন এসব আদর্শ হল দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাবনা। যে মুহূর্তে জাতি যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে — তখন এগুলো শুধু জাতির মনের জোরই কমিয়ে দেবে; সুতরাং এসব চিন্তা-ভাবনা ঝেড়ে ফেলে দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। একমাত্র এটাই দৃশ্যমান যার দ্বারা সংগ্রামে রত একটা জাতিকে বিচার করা যায়।
মানুষের অনুভূতি সম্পর্কে মন্টেকের অভিমত হল যুদ্ধের সময় সবচেয়ে অপ্রয়োজনীয় হল যত সত্বর সম্ভব মত স্থির এবং যত নির্দয়ভাবে যুদ্ধ করা যায়–সেটাই হয় মনুষ্যত্বের সবচেয়ে বড় পরিচয়। যখন কেউ এর উত্তরে রুচিবিজ্ঞান ইত্যাদি বড় বড় কথা বলে, তখন তার একটাই উত্তর দেওয়া সম্ভব। যুদ্ধের সময়ে অস্তিত্বরক্ষাটাই হল সবচেয়ে বড়, তখন অন্য কোন বিষয়ের কথা উল্লেখ করাই উচিত নয়। দাসত্বের জোয়াল হল যা সব সময় কাঁধে চেপে বসে থাকে। এটাই হল মানুষের জীবনের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতা যা তাকে একরকম বাধ্য হয়েই সহ্য করতে হয়।
সোয়াবিঙ* ক্ষয়শীলেরা কি জার্মানির আজকের ভাগ্য সম্পর্কে আশাবাদী? অবশ্য কেউই এ প্রশ্নটাকে ইহুদীদের সঙ্গে আলোচনা করতে বলতে বলবে না, কারণ তারা হল আজকের তথাকথিত সাংস্কৃতির সুগন্ধের আবিষ্কারক। তাদের অস্তিত্বই হল ঈশ্বরের সৃষ্টির সবচেয়ে দেহধারী ব্যতিক্রম।
যুদ্ধের সময় এসব আদর্শ যা সুন্দর এবং মানসিকগুণে সমৃদ্ধ তার কোন স্থান নেই। তারা যুদ্ধের প্রচারকার্যের উপযুক্ত মালমশলাও নয়।
যুদ্ধ চলাকালে প্রচারকার্য হল সেই যুদ্ধের শেষকথা। এবং এ সমাপ্তি হল জার্মান জাতির অস্তিত্বরক্ষাও শেষ পর্যায়। সুতরাং প্রচারকার্যের প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দেশ্য এ দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা উচিত। সবচেয়ে নিষ্ঠুর অস্ত্রই হল এক্ষেত্রে সবচেয়ে মানবীয়তার গুণে সমৃদ্ধ, অবশ্য যদি তারা সেই যুদ্ধ দ্রুত শেষ করতে সাহায্য করে। এবং সেইসব পদ্ধতিই সুন্দর এবং সম্মানীয় যা জাতির ঐতিহ্য এবং স্বাধীনতা বজায় রাখে। সম্ভবত এ মনোভাব নিয়েই এ জীবন-মৃত্যু যুদ্ধের প্রচারকার্য চালানো উচিত।
যদি এ জিনিসগুলোই তাদের শাসকবর্গকে বলা হয়, — এবং তারা যদি বুঝতে পারে তবে যুদ্ধের প্রচারকার্য কি ধরনের এবং কোথায় হবে এ নিয়ে অস্ত্র হিসেবে এটাকে ব্যবহার আর দ্বিধা দেখা দেবে না।
কারণ এ প্রচারকার্য আর কিছুই নয় একটা বিশেষ অস্ত্র, যারা এর সঠিক ব্যবহার জানে তাদের হাতে এ অস্ত্রই ভয়ংকর হয়ে ওঠে।
দ্বিতীয় প্রশ্ন হল এর চূড়ান্ত প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে : প্রচারকার্য কাদের উদ্দেশ্যে চালানো উচিত?
প্রচারকার্যের লক্ষ্য হওয়া উচিত সুবিশাল জনতা। বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় অথবা যাদের আজকে বদ্ধিজীবি বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাদের কাছে নিছক প্রচারকার্য চলে না; তাদের জন্য প্রয়োজন এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। তবে প্রচারকার্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ, যেমন ক্ষীণ শিল্পকলার সঙ্গে প্রাচীরপত্রের–এর সংবাদ বহনের ক্ষমতার দিকটার বিবেচনায় প্রাচীরপত্রের বিজ্ঞাপনে শিল্পীর দক্ষতার প্রকাশ হল তার রেখায় রঙের বৈচিত্রে কত লোককে তা আকর্ষণ করে। যত বেশি লোক আসে–প্রাচীরপত্রের বিজ্ঞাপন তত ভাল বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। যদি জনসাধারণকে এটা আকর্ষণ করে থাকে, তবু কিছুতেই এটাকে শিল্পের পর্যায়ে ফেলা যায় না। প্রাচীরপত্র শিল্প প্রদর্শনীতে শিল্পের বিকল্প কখনই নয়। সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং যারা শিল্প নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে উৎসুখ, তাদের প্রাচীরপত্র দিয়ে ইচ্ছা পূরণ করা সম্ভব নয়, তারজন্য অন্য কিছুর দরকার। সত্যিকথা বলতে কি, এ উদ্দেশ্য প্রদর্শনী গ্যালারীতে ঘোরাফেরা করার কোন অর্থই হয় না। শিল্পের ছাত্রদের প্রতিটি প্রদর্শিত ছবি খুঁটিয়ে দেখা উচিত, যাতে ধীরে ধীরে তার ভেতর একটা বিচার শক্তি গড়ে ওঠে। ব্যাপারটা প্রচারকার্যের ব্যাপারও একই।
প্রচারকার্যের উদ্দেশ্য কোন এক ব্যক্তিবিশেষের জন্য নয়, জনসাধারণের বিশেষ কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই হল এর কাজ; একমাত্র এ পথেই তা জনসাধারণের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব।
এখানে প্রচারকার্যের শিল্প কুশলতা এত পরিষ্কার এবং জোর করে মানুষের মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়া যায়, যা তাদের মনে একটা বিশেষ মতবাদের বিষয়টার বাস্তবতা সম্পর্কে গড়ে তোলে, তার প্রয়োজনীয়তা এবং চারিত্রিক দিকটার সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা তার উপলব্ধি করতে পারে।
যেহেতু এ শিল্প এখানেই শেষ নয়, কারণ এর উদ্দেশ্য হল প্রাচীরপত্রের বিজ্ঞাপনের মত; যার দ্বারা সুবিশাল জনসাধারণকে আকর্ষণ করা হয়। ব্যক্তিগত কোন একজনের জন্যে নয়, যে ইতিমধ্যে বিষয়টা সম্পর্কে একটা ধারণা নিয়ে বসে আছে। অথবা বিষয়টাকে বস্তৃতান্ত্রিক দিক দিয়ে বিচার করে একটা ধারণায় উপনীত হতে চায়–কারণ প্রচাররকার্যের উদ্দেশ্যই সেটা নয়। এর আবেদন হওয়া উচিত জনসাধারণের অনুভূতির কাছে, বিচারবুদ্ধির কাছে নয়।
সমস্তরকম প্রচারকার্য জনপ্রিয় উপায়ে পরিবেশন করা উচিত এবং এর বুদ্ধিমত্তার দিকটাও এমনভাবে ঠিক করা উচিত যা অপেক্ষাকৃত কম বুদ্ধিসম্পন্ন জনসাধারণকে ছুঁতে পারে, কারণ এদের উদ্দেশ্যই তো প্রচারকার্য চালানো। সুতরাং এর বুদ্ধিমত্তার দিকটা এমন হওয়া উচিত যাতে সাধারণ জনসাধারণের মধ্যে এটা পৌঁছতে পারে। যখন একটা পুরো জাতিকে এর আওতায় আনা প্রয়োজন, বিশেষ করে যুদ্ধের প্রচারকার্যের সময়ে, তখন উচ্চ বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন নেতাকে এড়াবার জন্য এত বেশি মনযোগ দেওয়ার প্রয়োজন নেই, কারণ একটা দল সবসময়ই থাকে যারা সাধারণের চেয়ে অধিক যুক্তিসম্পন্ন।
যত বেশি বৈজ্ঞানিক প্রচলিত ধারায় এবং যত বেশি পরিমাণে তা’ জনতার অনুভূতির উদ্দেশ্যে প্রচারিত করা হবে, তত চরম সাফল্য আসবে। প্রচারকার্যের সত্যিকারের মূল্যায়ন এতেই নিহিত, ছোট্ট বুদ্ধিমত্তা বা শিল্পপ্রেমিক গণ্ডীতে নয়।
প্রচারকার্যের শৈল্পিক দিকটা হল–যার দ্বারা এটা জনসাধারণের কল্পনার দিকটা তাদের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে জাগাতে পারে। এর মনস্তত্বের দিকটার গড়ন এমনভাবে হওয়া উচিত যা জাতীয় স্তরে গিয়ে আবেদন জানাতে সক্ষম হয়। এ ব্যাপারটাই আমাদের মধ্যে যাদের বুদ্ধি একেবারে উচ্চস্তরের তারা বুঝতে পারে না, এটাই হল তাদের মানসিক গর্ব বা জড়তার একটা প্রকৃষ্ট প্রমাণ।
একবার যদি আমরা বুঝতে সক্ষম হই যে এ প্রচারকার্যের প্রবৃত্তিজনক শক্তি কত তীব্র জনসাধারণের ভেতরে, তবে নিচের ফলাফলগুলো আমরা প্রত্যক্ষ করব :
প্রচারকার্যের সংগঠন এবং প্রচার এমনভাবে হওয়া উচিত নয় যে এটা মনে হবে বহু প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সমন্বয়ে গঠিত।
জনসাধারণের ধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত পরিসীমিত; এবং তাদের বোঝার ক্ষমতাও দুর্বল। অপরদিকে, তারা যে কোন ব্যাপারে দ্রুত ভুলে যায়। এরকম ক্ষেত্রে, সমস্ত প্রকার কার্যকরী প্রচারকার্যের গণ্ডী কয়েকটা অতি প্রয়োজনীয় ব্যাপারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। এবং যার বহিঃপ্রকাশ হবে বাঁধা ধরা ছকে। এ শ্লোগান ক্রমাগত আবৃত্তি করে যেতে হবে,–যতক্ষণ না পর্যন্ত শেষ মানুষটা এর আওতায় আসে। যদি এ আদর্শকে তুলে বা প্রচারকার্যকে বিমূর্ত এবং সাধারণভাবে উপস্থিত করা হয়, তবে তা কোন কাজেই আসবে না–কারণ জনসাধারণ তা বুঝতে বা মনের ভেতরে ধরে রাখতে সক্ষম হবে না–যে উদ্দেশ্যে প্রচারকার্য চালানো হচ্ছে। সুতরাং সংবাদের পরিব্যপ্তি অনুসারে ধরন-ধারণ, পরিকল্পনা নির্ধারিত করা উচিত, যাতে মনস্তত্ত্বের দিক থেকে এটা প্রচণ্ড রকমের কার্যকরী হতে পারে।
কিন্তু এ শিল্প এখানেই শেষ নয়। কারণ এর উদ্দেশ্য হল একেবারে সেই বিজ্ঞাপনের প্রাচীরপত্রের মত, যার কাজ হল জনতাকে আকর্ষণ করা এবং যাদের ইতিমধ্যেই ব্যাপারটা সম্পর্কে একটি ধারণা সুসংগঠিত হয়েছে বা যারা ইতিমধ্যেই এর বস্তৃতান্ত্রিক দিকটার প্রতি আকৃষ্ট তাদের জ্ঞান বিতরণ–কারণ প্রচারকার্যের উদ্দেশ্য তা নয়; এ প্রচারকার্যের আবেদন হবে জনতার অনুভূতির কাছে, বিচার বুদ্ধির নিকটে নয়।
সমস্ত রকমের প্রচারকার্য জনপ্রিয় উপায়ে পরিবেশন করা উচিত। এবং এর বুদ্ধিমত্তার দিকটা এমন হওয়া উচিত যাতে সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন লোকদের এটা আকৃষ্ট করতে পারে। কিন্তু তার বুদ্ধিমত্তার কিছুটা এমন হওয়া চাই যাতে অতি অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন জনতাও এটাকে উপলব্ধি করতে পারে; যাদের উদ্দেশ্যে এ প্রচারকার্য চালানো হচ্ছে। যখন পুরো একটা জাতিকে অখণ্ডভাবে এ প্রচারকার্যের ভেতরে আনার প্রয়োজন, যেটা বিশেষ করে যুদ্ধের প্রচারকার্যের আবশ্যক হয়ে পড়ে, তখন উচ্চ বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন লোকদের এর আওতার বাইরে রাখার জন্য অত বেশি সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন নেই।
প্রচারকার্যের এ বৈজ্ঞানিক প্রচলিত ধারার এবং যত বেশি পরিমাণে এটা জনসাধারণের অনুভূতিকে লক্ষ্য করে প্রচারিত করা হবে,–এর সাফল্যও তত চূড়ান্ত হবে। প্রচারকার্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার এ-ই হল চরম মূল্য। মুষ্টিমেয় শিল্পী বা বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জনসাধারণের অনুমোদন নয়।
প্রচারকার্যের শৈল্পিক দিকটা হল জনসাধারণের ঘুমিয়ে থাকা কল্পনার সূক্ষ্ম দিকটাকে আবেদন দ্বারা জাগিয়ে তোলা; তার জন্য মনস্তত্ত্বের সেই বিশেষ দিকটাকে খুঁজে বার করা দরকার, যা জাতির জনসাধারণের হৃদয় অধিকার করতে সমর্থ হবে, শুধু আমাদের মধ্যে তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন, তাদের জন্য নয়। কারণ এ সচেতন বুদ্ধিসম্পন্নতা আর কিছুই নয়, নিজেদের সম্পর্কে গর্ব অথবা মানসিক জড়তার লক্ষণ।
একবার যদি আমরা বুঝতে পারি যে এ প্রচারকার্যের প্রবৃত্তিজনক ক্ষমতা জনতার মধ্যে কতখানি সুদূর প্রসারী, তবে নিচের শিক্ষাগুলো তা থেকে পেতে পারি :
প্রচারকার্যের সংগঠন বা পরিচালন এমন হওয়া উচিত নয় যাতে এটা অনেক প্রকারের বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত বলে মনে হয়।
জনসাধারণের ধারণ ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ; এবং তাদের বোঝার ক্ষমতাও দুর্বল। অপরদিকে তাদের স্মৃতিশক্তি প্রচণ্ডরকমের কম থাকার দরুন তারা সবকিছুই দ্রুত ভুলে যায়। এ কারণে সমস্ত রকমের প্রয়োজনীয় ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। এবং সেগুলোকে যতখানি সম্ভব একই প্রকারে পুনরাবৃত্তি করা উচিত। এসব ধ্বনি ক্রমাগত পুনরাবৃত্তি করে যেতে হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না শেষ ব্যক্তিটি এ প্রচারকার্যের উদ্দেশ্যের কজায় এসে ধরা দেয়। এ আদর্শ ভুলে গেলে এ প্রচারকার্যের সমস্ত রকম উদ্দেশ্যই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। কারণ জনসাধারণের পক্ষে তাকে যা বলা হয়েছে তা হজম করা বা মনে রাখা সম্ভব হয়ে উঠবে না। সুতরাং প্রচারকার্যের গুরুত্ব বুঝে নিয়ে তাকে। এমনভাবে প্রচার করা উচিত যাতে জনসাধারণের মনস্তত্ত্বের দিকটাকে এটা সম্পূর্ণভাবে আকর্ষণ করতে পারে।
উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, শক্রদের মূল্যায়ণ ব্যাঙ্গাত্মক উপায়ে করা ভুল, যা অস্ট্রিয়ায় জার্মানদের পত্রিকাগুলো প্রচারকার্যের উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করেছিল। এ আদর্শগত দিকটাই হল ভুল; কারণ যখন তারা যুদ্ধের সময় শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়ায়, তখন আমাদের সৈন্যদের ধ্যান-ধারণা আলাদা ছিল ওদের সম্পর্কে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত ওই ভুলের মাশুল বিধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যখন জার্মান সৈন্যরা বুঝতে পারে যে তাদের বিরোধী পক্ষের সৈন্যরা যথেষ্ট পরিমাণে সুশিক্ষিত, তখন তারা উপলব্ধি করে যে ভুল সংবাদ দ্বারা তাদের প্রতারণা করা হয়েছে। তাই তাদের সংগ্রাম শক্তিকে উদ্বুদ্ধ এবং শক্তিশালী করে তোলার চেয়ে এ সংবাদের কার্যকারীতা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। সমস্ত উৎসাহটা ভেঙে পড়ে।
অপরদিকে বৃটিশ এবং আমেরিকান যুদ্ধের প্রচারকার্যের মনস্তত্ত্বের দিকটা যথেষ্ট পরিমাণে অভিজ্ঞ ছিল। জার্মান সৈন্যদের বর্বর এবং হুণদের মত নিষ্ঠুরভাবে চিত্রিত করে তাদের নিজেদের সৈন্যদের যুদ্ধের বর্বরতা এবং নির্দয়তার বিরুদ্ধে সুযোগ্য করে তুলেছিল। যার জন্য তাদের মধ্যে মিথ্যা স্বপ্ন বলতে কিছু ছিল না। যুদ্ধক্ষেত্রে যেসব ভয়াবহ অস্ত্রের মুখোমুখি তাদের হতে হয়েছে–তার সংবাদ নিজেদের সরকারের মাধ্যমে আগেই তারা পেয়েছে। সুতরাং সরকারের সততায় তারা আরো অধিক পরিমাণে আস্থা রেখেছে। এ প্রকারে তাদের প্রচণ্ড ক্রোধ এবং ঘৃণা এ কুখ্যাত বিরুদ্ধপক্ষের সৈন্যদের ওপর গিয়ে পড়েছে। জার্মান যুদ্ধাস্ত্রর যে ভয়াবহ ফলাফল হয়েছে, যা তাদের কাছে জার্মানদের এ হুণ এবং বর্বর রূপেই প্রতিফলিত হয়েছে, যেটা সরকারের প্রচারকার্যের মাধ্যমে তাদের আগে থেকেই জানা ছিল। অপরদিকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রীভাবের কারণে তাদের অস্ত্রে যে ভয়াবহতা সৃষ্টির পক্ষে সক্ষম তা মিথ্যা। দুর্ভাগ্যবশতঃ, জার্মানদের ক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টোটা ঘটেছে–যারা শেষ পর্যন্ত ঘরের সংবাদকে দলবাজী আর প্রতারণা বলে বাতিল করে দিয়েছে। এ ধরনের ফলাফল সম্ভব হয়েছিল কারণ দেশের সরকার এ প্রচারকার্যকে গর্দভ মস্তিষ্কের বেশি মূল্য দেয়নি এবং তাদের ধারণাই ছিল না যে প্রচারকার্যের জন্য নিপূণ বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন যা খুঁজে বের করতে হয়।
কিভাবে প্রচারকার্য চালাতে নেই–জার্মান যুদ্ধের প্রচারকার্য হল তার অতুলনীয় উদাহরণ এবং মনস্তত্বের দিক থেকে এটা একটা চরম ব্যর্থতার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তও বটে।
তবে যাদের চোখ খোলা ছিল, তারা শত্রুদের নিকট এ বিষয়ে অনেক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পেয়েছিল; যাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্যরূপ তখনো কঠিন হয়ে ওঠেনি এবং যারা সুদীর্ঘ সাড়ে চার বছর ধরে শক্রর প্রচারকার্যের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল।
সবচেয়ে দুঃখের বিষয় আমাদের লোকেরা প্রচারকার্যের সেই প্রথম কারণগুলোই বুঝতে পারেনি, যা প্রতিটি প্রচারকার্যের পরিপূর্ণতার জন্য প্রয়োজন। বিশেষ করে প্রচারিত প্রতিটি সমস্যার শুধু একদিকটাকেই তুলে ধরতে হবে। কিন্তু এ বিষয়ে এত বিস্তর ভুল করা হয়েছে যুদ্ধের শুরু থেকেই যে সন্দেহাতীতভাবে এ বোকামী আমাদের লোকের মুখামীকে সরাসরি প্রমাণ করে।
উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, কয়েকটি নতুন ধরনের সাবানের বিজ্ঞাপনের অভিপ্রায়ের জন্য আমরা যে প্রাচীরপত্রের ব্যবহার করে থাকি, তাতে বিশেষ করে সাবানের চমৎকার দিকটা অবশ্যই তুলনামূলকভাবে অন্য ছাপ মারা সাবানের থেকে তুলে ধরা হয়ে থাকে না। এ বিষয়ে আমরা সবাই একমত হব; এবং রাজনৈতিক প্রচারকার্যও ঠিক এক ধারাতে চলে। প্রচারকার্যের লক্ষ্য সত্যকে সোজাসুজি উদঘাটিত করা নয়, কারণ তা তো অপর পক্ষের দিকে যাবে–আপাতদৃষ্টিতে যা তত্ত্বের দিক থেকে বিচার হয়ে থাকে। এটা শুধু সত্যের সেই দিকটাকেই প্রকাশ করবে যা নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় সাহায্য করবে।
কে যুদ্ধের উদ্যোক্তা, এ প্রশ্নের আলোচনায় যাওয়াটা হল গোড়াতেই ভুল এবং সেইসঙ্গে একক জার্মানির ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দেওয়াটাও উচিত নয়–এটাকে প্রমাণ করতে যাওয়াটাও বোকামী। কোনরকম আলোচনা ছাড়াই যুদ্ধ শুরু করার পুরো দোষটা শর্কর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া উচিত।
এবং এ অর্ধ-সত্যের পরিণতিটা কি? সাধারণ সুবিশাল জনতা কুটনীতিজ্ঞ বা অধ্যাপক নয় যে জনসাধারণের ব্যবহার সম্পর্কে তাদের জ্ঞান থাকবে। তাদের মধ্যে এমন জ্ঞানও নেই যার দ্বারা তারা নির্দিষ্ট মতামত গঠন করতে পারে। কিন্তু এ টলমলে মানব সন্তানরা ক্রমাগত এক আদর্শ থেকে, আরেক আদর্শে দোল খায়। যেইমাত্র আমাদের নিজেদের প্রচারকার্য কিছুমাত্র আভাস দেয় যে শত্রুপক্ষেরও কিছুটা বিচারবোধ আছে, তৎক্ষণাৎ আমাদের নিজেদের বিচারবোধ সম্পর্কেই প্রশ্ন উঠবে। শত্রুপক্ষের শেষ কোথায় বা কোথা থেকেই বা আমাদের দোষের শুরু হয়েছে–এ পার্থক্য বিচার করার মত ক্ষমতা জনসাধারণের নেই; এসব বিষয়গুলোতে তারা সন্দেহের দোলায় দোলে এবং অবিশ্বাসী হয়ে পড়ে। বিশেষ করে শত্রুরা যেখানে তাদের উপদেষ্টাদের ঘাড়ে ভুলের বোঝা চাপিয়ে দেয়। শক্রদের প্রচারকার্য যে কথাগুলো বলেছিল, এ ব্যাপারে তার চেয়ে আর বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে, যা সমানুপাতিক এবং ভারসাম্যের দিক থেকে আমাদের প্রচারের থেকে অনেক বেশি উন্নত এবং এগুলোই আমাদের জনসাধারণকে ক্ষিপ্ত করে তোলে, প্রত্যেক শত্রুপক্ষের ওপর অন্যায় করা হচ্ছে বলে ভাবে। এমন কি এ ধারণা এত প্রবল হয়ে ওঠে যে আমাদের জাতির এবং দেশের ধ্বংসের বিনিময়েও তাদের মনোভাব বদলায় না।
স্বভাবতই জনসাধারণ সত্যের এদিকটাতে একেবারেই সচেতন ছিল না। এমন কি তথাকথিত বিশেষজ্ঞরা বিষয়বস্তুটাকে এ দৃষ্টিকোণ থেকে কখনই বিচার করে দেখেনি।
জাতির মধ্যকার বিরাট একটা অংশ চারিত্রিক দিক থেকে স্ত্রীজনোচিত ছিল এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভাবালুতার দ্বারা পরিচালিত, তীক্ষ্ম যুক্তির স্থান সেখানে কোথায়! এ ভাবালুতা কিন্তু জটিল মানসিকতার জন্য নয়। এটা প্রচণ্ড রকমের প্রভেদবুদ্ধিসম্পন্নও নয়। কিন্তু শুধু ভালবাসা বা ঘৃণার প্রতি ইতিবাচক ও নৈতিবাচক ধ্যান ধারণা, যেটা নির্ভুল এবং ভুল, সত্য এবং মিথ্যায় মিশ্রিত। এ ধ্যান ধারণার অর্ধেকটা এরকম, বাকি অর্ধেকটা কিন্তু সেরকম নয়। ইংরেজদের প্রচারকার্য বিশেষ করে এ দিকটাকে চমৎকারভাবে বুঝেছিল এবং সে কারণে অত সুন্দরভাবে তা ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োগেও সমর্থ হয়েছিল।
তারা ব্যাপারটায় কোনরকম দ্বিধার মনোভাব নিয়ে এগোয়নি। যে কারণে কারোর মনে কোনরকম সন্দেহেরও উদ্রেক হয়নি।
জনসাধারণের এ ভাবালুকতার দিকটা যে তারা কত চমষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছিল তার একটা অসাধারণ উদাহরণ হল— তারা শত্রুপক্ষকে যেভাবে বীভৎস এবং নির্দয় বলে চিত্রিত করেছিল বাস্তবে যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের বর্ণনার সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটা হুবহু খাপ খেয়ে গিয়েছিল। সেই কারণে যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের সৈন্যদের একতাবদ্ধতা আরো বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, যা চরম পরাজয়ের ক্ষেত্রেও বজায় ছিল। উপরন্তু, কাঠের তৈরি যন্ত্রণাদায়ক যন্ত্রবিশেষের মত তারা তাদের শক্ত অর্থাৎ জার্মানদের চিত্রিত করেছিল। ওদের প্রচারকার্যে যুদ্ধের সমস্ত দায়িত্ব যাদের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা শুধু নির্দয় বা নিছক মিথ্যাতে পূর্ণ ছিল না, যেভাবে গাণিতিক ছকে বেঁধে তা জনসাধারণের কাছে উপস্থাপনা করা হয়েছিল, জনতা পরিপূর্ণভাবেই তা বিশ্বাস করেছিল। কারণ জনসাধারণের ভাবালুতা সব সময়েই শেষ পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়। এবং সেই কারণেই এ নিছক মিথ্যাকেও তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে।
এ প্রচারকার্যের কার্যকারীতা এত সুন্দর এবং তীক্ষ্মতার সঙ্গে হয়েছিল যে শুধু যুদ্ধের সুদীর্ঘ সাড়ে চার বছর নয়, আজ পর্যন্ত আমাদের দেশের লোকেদের মননশীলতা এবং বিষয়ের প্রতি একাগ্রতা তা অনেক পরিমাণে কমিয়ে দিয়েছে।
আমাদের প্রচারকার্য যে একই রকমের সফলতা লাভ করতে পারেনি, তার জন্য আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কারণ আমাদের প্রচারকার্যের দ্বিধার ভাবের মধ্যেই সে ব্যর্থতার বীজ ছিল। এবং বিষয়বস্তুর অসারত্বই তা জনসাধারণকে মনপ্রাণ দিয়ে সত্য বলে গ্রহণ করতে দেয়নি। একমাত্র আমাদের লক্ষ্যশূন্য রাষ্ট্রনেতারা কল্পনা করত যে তাদের শান্তিবাদীতার আশা উপচে পড়ে এ ধরনের উৎসাহের মূলে জল দিয়ে মানুষকে তার দেশের জন্য মৃত্যুর জন্য পর্যন্ত অনুপ্রাণিত করবে।
সুতরাং আমাদের সৃষ্ট বিষয়বস্তু যে শুধু অসার ছিল তা-ই নয়, ক্ষতিজনকও বটে।
এসব প্রচারকার্যের সঙ্গে যত বেশি প্রতিভাবান ব্যক্তিকেই জড়ো করা হোক না কেন, নিচেকার আদর্শগুলোকে এ সুরে বাঁধতে না পারলে তার কোন অর্থ-ই হবে না। প্রচারকার্যের গঞ্জ বিশেষ কয়েকটা চিন্তাধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত, এবং বারে বারে তাই পুনরাবৃত্তি সাপেক্ষ; এখানে, অন্যান্য অসংখ্য ক্ষেত্রের মত ধৈর্যই হল প্রথম এবং সর্বোত্তম সোপান সাফল্য লাভ করার পক্ষে।
বিশেষ করে প্রচারকার্যের ক্ষেত্রে, মার্জিত রুচি এবং উজ্জ্বল বুদ্ধিমত্তাকে কখনই সামনে স্থান দেওয়াটা উচিত হবে না। কারণ এ গুণগুলো থাকলে তারা সত্যিকারের প্রচারকার্যের গুণগুলোর স্রোতকে সাহিত্যাশ্রয়ী করে তা চায়ের আসরের উপযোগী করে তুলবে। জনতার দ্বিতীয় শ্রেণী সম্পর্কে একটা ধারণাকে সব সময় মনে রাখতে হবে যে: সাধারণ ব্যাপারগুলো তাদের মধ্যে কোন উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারে না। তাই তারা নিত্য নতুন উত্তেজনার খোরাকের জন্য সর্বদা উদগ্রীব হয়ে ঘুড়ে বেড়ায়।
এসব লোকেরা সব বিষয়েই অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ক্লান্ত এবং আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে। তাই তারা সর্বদাই কোনরকম পরিবর্তন চায়; এবং সেই পরিবর্তনের মাধ্যমে তাদের নিকটজনদের বোকামী থেকে নিজেদের দূরে রাখতে ব্যস্ত থাকে। এমন ভাবসাব করে যে পুরো ব্যাপারটা তারা একাই বোঝে। তথাকথিত উজ্জ্বল বুদ্ধিমানরাই হল প্রচারকার্যের প্রথম এবং প্রধান সমালোচক। নিপুণভাবে বলতে গেলে তাদের ভাবধারাই এ ব্যাপারে বিশেষভাবে দায়ী। কারণ তাদের কাছে পুরো ব্যাপারটাকে আদিম বলে মনে হয়। তারা সবসময়েই নতুন কিছু খোঁজে ফিরে। এজন্যেই তারা জনতাকে সুপরিকল্পিত উপায়ে অনুপ্রাণিত করার যে কোনরকম পন্থারই চিরন্তন শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। যে মুহূর্তে প্রচারকার্য তাদের রুচিসম্মত হয়, সে মুহূর্তে তা অসংলগ্ন হয়ে টুকরো আকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।
এ তথাকথিত দ্রসম্প্রদায়ের মনতুষ্টি এবং নানা ধরনের চিন্তাধারায় পরিবর্তন আনা এ প্রচারকার্যের উদ্দেশ্য নয়। এর সর্বপ্রধান কাজ হল জনসাধারণকে স্বমতে আনা যাদের ধীরবুদ্ধির জন্য যে কোন জিনিস বুঝতে যথেষ্ট সময় নিয়ে থাকে; একমাত্র ক্রমাগত পুনরাবৃত্তিই সেই জনসাধারণের স্মৃতিতে ব্যাপারটা খোদাই করে দিতে পারে।
প্রচারকার্যের প্রতিটি বার্তার ব্যাখ্যার শেষ সেই একবিন্দুতে; অবশ্য সামনের চিৎকারগুলো বিভিন্ন ধরনের এবং রকমারী দৃষ্টিকোণ থেকে করা একমাত্র এ উপায়ে প্রচারকার্যের দৃঢ়বদ্ধতা এবং গতিময়তা প্রকাশ পাওয়া সম্ভব।
এ পদ্ধতি ধরে এবং তাতে লেগে থেকে দৃঢ়তা এবং সংক্ষিপ্ত উপায়ে এগিয়ে গেলেই শেষে সাফল্য আসতে বাধ্য। এরই পুরস্কারস্বরূপ সে হঠাৎ এবং অবিশ্বাস্য ধরনের সাফল্যের দ্বারে গিয়ে উপস্থিত হবে।
যে কোন বিজ্ঞাপনের, তা রাজনৈতিক বা ব্যবসায়িক যা-ই হোক না কেন তার সাফল্য নির্ভর করে ক্রমাগত এবং কতখানি ধৈর্যের সঙ্গে তা সম্পাদিত হয়েছে।
এ ব্যাপারেও আমাদের শত্রুরা প্রচারকার্যের সংঘবদ্ধতার চমৎকার উদাহরণ স্থাপন করে। এটা মাত্র কয়েকটা বিষয়বস্তু ঘিরে ছিল–যা বিশাল জনসাধারণের উপযোগী এবং ব্যাপারগুলোকে পুনরাবৃত্তি করা হচ্ছিল ধৈর্যের সঙ্গে একবার যখন বিষয়গুলো এবং যেভাবে তাদের উপস্থাপনা করা হচ্ছে তা পৃথিবী স্বীকার করে নেয়, তখন জনসাধারণই তাতে দৃঢ় সংলগ্ন হয়ে লেগে থাকে। হ্যাঁ, সমস্ত যুদ্ধকাল ধরে। প্রথম দৃষ্টিতে এটাকে বোকামী বলে মনে হলেও পরে মনে হবে সমস্ত ব্যাপারটাই বিরক্তি উৎপাদক; কিন্তু শেষে সবাই বিশ্বাস করবে।
কিন্তু ব্রিটিশ ব্যাপারটায় আরো বেশি কিছু বুঝত। এ অশরীরী অস্ত্রের সাফল্য জনসাধারণের ভেতরে কত গভীরে, এবং কখন তা সময় মত টেনে বার করতে হবে যাতে একটা বিশাল খরচের বিরাট অংশ উদ্ধার করা যায়।
ইংল্যান্ডে প্রচারকার্যকে প্রথম শ্রেণীর হাতিয়ার বলে গণ্য করা হয়, অথচ আমাদের দেশে বেকার রাজনীতিজ্ঞদের কাছে এটা হল শেষ আশার আশ্রয় এবং কর্তব্য পরাজুখ ব্যক্তির কাছে এটা হল আঁটসাট ও উষ্ণ ধরনের নায়কোচিত কাজকর্ম।
সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখলে ব্যাপারটার ফলাফল দাঁড়িয়েছিল নেতিবাচক।
———–
* সোয়াবিঙ হল মিউনিকের শিল্পীদের আস্তানা, যাতে তাদের ছবি আঁকার স্টুডিও আর পড়াশোনার জায়গা — বিশেষ করে যাযাবর শিল্পীদের।
০৭. রাষ্ট্রবিপ্লব
১৯১৫ সালে শত্রুরা আমাদের সৈন্যদের মধ্যে প্রচারকার্য শুরু করে। ১৯১৬ সাল থেকে ক্রমাগত এটার বিস্তার হতে থাকে, এবং ১৯১৮ সালের শুরুতে এটা ফুলে ফেঁপে বন্যার আকার ধারণ করে। এখন কোন একজনের পক্ষে এ ধর্মান্তরিতের কাজের সুদূর প্রসারী ফলাফলের ধাপ বেয়ে বেয়ে এগনো সহজ। ধীরে ধীরে আমাদের সৈন্যরা শত্রুপক্ষ যেভাবে চায়, ঠিক সেইভাবে চিন্তা করতে শুরু করে। জার্মানদের পক্ষ থেকে এর বিরোধিতা করার জন্য কোনরকম প্রচারকার্যের ব্যবস্থা ছিল না।
জার্মান সৈন্যধ্যক্ষরা মনস্তত্বের দিক থেকে ভুল করত যদি তারা মানসিক শিক্ষা দেওয়ার কাজে হাত দিত। নিশ্চিত ফলপ্রদ ব্যাপার হিসেবে এটা ঘরোয়া নীতি। কারণ তারাই এতে সাফল্য লাভ করতে সক্ষম যারা চার বছর ধরে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে বীরের মত অশেষ কষ্টবরণ করেছে। কিন্তু তখন আমাদের দেশের লোকেরা কি করেছিল? এটা কি বুদ্ধিমত্তার অভাব নাকি বিশ্বাস না থাকার দরুণ এ অসাফল্য?
১৯১৮ সালের গ্রীষ্মের মাঝামাঝি; মারণে নদীর দক্ষিণ তীর থেকে পশ্চাদ অপসারণের পর জার্মান সংবাদপত্র যে নীতি গ্রহণ করেছিল তা এত মোটা এবং অপদার্থ বোকার মত ছিল যে আমি নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করতাম এবং যা দিনের পর দিন আমাকে ক্রুদ্ধই করে তুলেছিল। এটা কি সত্যি যে আমাদের মধ্যে সত্যিকারের সাহসী বলতে কি কেউ-ই ছিল না, যে এ ধরনের পেছন থেকে ছুরি মারার হাত থেকে আমাদের নায়কোচিত সৈন্যদের রক্ষা করতে পারে।
১৯১৪ সালের সে দিনগুলোতে ফ্রান্সে কি হয়েছিল, যখন আমাদের সৈন্যদল সে দেশ আক্রমণ করে একের পর এক যুদ্ধে জিতে এগিয়ে চলেছিল? ইতালির কি হয়েছিল—যখন তাদের সৈন্যদল ইজানো ফ্রন্টে বিধ্বস্ত? ১৯১৮ সালের বসন্তকালে ফ্রান্সে আবার কি হয়েছিল— যখন জার্মান সৈন্যদল ফ্রান্সের সৈন্যদের হটিয়ে দিয়ে মূল ঘাঁটিগুলোকে ঝড়ের গতিতে দখল করে বসেছিল এবং দূর পাল্লার জার্মান কামান সমানে পারীর ওপরে গোলাবর্ষণ করে চলেছিল?
কী করে এসব সৈন্যদলের মাথা উঁচু করা সাহস এবং জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস একটা ফুকারে নির্ভিয়ে দেওয়া হয়েছিল?
কিভাবে তাদের প্রচারকার্য এবং জনসাধারণকে সচেতন করার সুন্দর পদ্ধতিটাকে কাজে না লাগিয়ে যুদ্ধে নিশ্চিত জয়ী সৈন্যদের মাথার ওপরে খড়গাঘাত হেনেছিল।
ইতিমধ্যে আমাদের লোকেরা সেই জায়গায় কি করছিল? কিছুই নয়। বারে বারে আমি রোষান্বিত এবং ক্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলাম, বিশেষ করে শেষের দিকের সংবাদপত্রগুলো পড়ে যা’তে বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া ছিল কিভাবে তা জনসাধারণ এবং সৈন্যদের মধ্যে জড়তা জাগিয়ে তুলে নিধন যন্ত্র চালিয়ে চলেছে। এ চিন্তায় যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়েছি যে জার্মানদের প্রচারকার্যের ভার যদি আমার হাতে থাকত, (এসব অনুপযুক্ত অপরাধী বিশেষ নির্বোধ ব্যক্তি এবং দুর্বল প্রাণীদের হাতে না থেকে), তবে হয়ত সম্পূর্ণ চিত্রটাই অন্যরকম হত।
সেই মাসগুলোতে আমি অনুভব করেছিলাম যে আমাকে সীমান্তে যুদ্ধরত রেখে ভাগ্য আমার প্রতি বিরূপ খেলা খেলছে; এবং সেখানে দাঁড়িয়ে আমাকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হচ্ছে, সেখানে একটা নিগ্রো বা যে কারোর গুলি এসে আমাকে ইহকালের মত স্তব্ধ করে দিতে পারে, অথচ পিতৃভূমির জন্য অন্য জায়গাতে অনেক বেশি কাজ করতে সক্ষম। আমার নিজেরও যথেষ্ট পরিমাণে আত্মবিশ্বাস বর্তমান যে প্রচারকার্যের ব্যাপারটা আমি সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করতে পারি।
কিন্তু আমার পরিচিত বলতে তো কিছু ছিল না, আট লক্ষ্য সৈন্যের মধ্যে আমি সাধারণ একজন সৈনিক মাত্র। সুতরাং আমার পক্ষে চুপচাপ মুখ বন্ধ রেখে আমাকে যে কর্তব্য সম্পাদনা করতে দিয়েছে সেটা করে যাওয়াই যুক্তিযুক্ত।
১৯১৫ সালের গ্রীষ্মে আমাদের পরিখায় শত্রুপক্ষের প্রথম প্রাচীরপত্র পড়ে; তাদের প্রায় সবই এক ধাচের গল্প। শুধু আঙ্গিকেই যা কিছু একটু পরিবর্তন। গল্পটা হল জার্মানির দুঃখ দিনে দিনে জয়ের সম্ভাবনাটাও মলিন হয়ে আসছে। ঘরের লোকদের শান্তি এবং সন্ধির ইচ্ছা তীব্র হয়ে উঠেছে; কিন্তু সামরিক কর্তৃপক্ষ এবং কাইজারের জন্য তা বোঝার উপায় নেই। সমস্ত পৃথিবী জানত এ যুদ্ধ জার্মান জনসাধারণের জন্য শুধু হয়নি, হয়েছে কাইজারের ইচ্ছায়। তার জন্য জার্মান জনসাধারণও দায়ী নয়। দায়ী যদি কাউকে করতে। হয় তবে সে হল কাইজার; এবং যতদিন না পর্যন্ত পৃথিবীর শান্তির এ শত্রু কাইজারকে দূর করা হবে — ততদিন পর্যন্ত শান্তি আসার কোন উপায়ই নেই।
কিন্তু যুদ্ধ শেষ হলেই উদার এবং গণতান্ত্রিক দেশগুলো জার্মানিকে বন্ধু হিসেবে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের কাজে সহযোগী করে নেবে। এ কাজটা করা হবে যে মুহূর্তে প্রুশিয়ার সামরিক বাহিনী শেষমেষ সমূলে ধ্বংস হবে।
এসব বক্তব্যকে সচিত্রিত এবং প্রমাণ করার জন্য, সেইসব প্রাচীরপত্রের প্রায়ই ‘বাড়ির চিঠি’ থাকত–যেগুলো শত্রুপক্ষের প্রচারকার্যের যথার্থতা প্রমাণের সহায়ক স্বরূপ। সত্যি বলতে কি, এত সব প্রয়াস দেখে আমরা হাসতাম। প্রাচীরপত্রগুলো পড়ে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে পাঠিয়ে দিতাম, তারপরে পুরো ব্যাপারটাই ভুলে যেতাম–যতদিন পর্যন্ত ভাল একটা হাওয়া আবার পরিখার ভেতরে প্রবাহিত না হত। এসব প্রাচীরপত্রগুলো বিশেষ করে বিমান থেকে ফেলা হত এবং তার জন্য বিশেষ ধরনের বিমানের ব্যবহার করা হত।
এ প্রচারকার্যের একটা মুখাবয়ব অত্যন্ত চমকপ্রদ। ব্যাভেরিয়ান সৈন্যদলের ভেতরে শদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ গড়ে তোলার ক্রমাগত একটা প্রচেষ্টা চলছিল; প্রুশিয় এবং প্রুশিয়ার সৈন্যরাই নাকি এ যুদ্ধ বাধাবার এবং এটাকে জিইয়ে রাখার জন্য মূলত দায়ী। এবং সে কারণেই শত্রুপক্ষের ব্যাভেরিয়ার সৈন্যদলের প্রতি কোনরকম বিরূপতা নেই। কিন্তু তাদের সাহায্য করারও কোন পথ খোলা ছিল না। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা প্রশিয়ানদের স্বার্থরক্ষা করে চলেছে এবং আগুন থেকে তাদের জন্য বাদাম তোলার কাজে নিযুক্ত।
এ ক্রমাগত প্রচারকার্যের ফলাফল ১৯১৫ সালে আমাদের সৈন্যদের ওপর সুদূর প্রসারী হয়। ব্যাভেরিয়ার সৈন্যদের মধ্যে প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে যথেষ্ট পরিমাণে বিক্ষোভ দানা বেঁধে ওঠে। কিন্তু যারা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, তারা এর কোনরকম প্রতিবাদ করতে সচেষ্ট হয়নি। পুরো ব্যাপারটা একটা ভয়ঙ্কর রকমের অপরাধ বিশেষ। কারণ তৎক্ষণাৎ বা পরে শুধুমাত্র প্রশিয়ানদের কপালেই লাঞ্ছনা জোটে না, সমস্ত জার্মান জাতিকেই সেই দুর্ভাগ্যের অংশ বাধ্য হয়ে বরণ করে নিতে হয়।
এভাবে ১৯১৬ সালের পর থেকে শত্রুপক্ষের প্রচারকার্য অভাবনীয় সফলতা লাভ করতে শুরু করে।
ঠিক এভাবে সৈনিকদের বাড়ি থেকে যেসব চিঠিপত্রাদি আসতে থাকে তার ফলাফল হয় সুদূর প্রসারী। সমস্ত ব্যাপারটা এমন এক অবস্থায় এসে দাঁড়ায় যে শত্রুপক্ষের আর এভাবে প্রচারপত্র ছড়ানোর প্রয়োজন পড়ে না। এবং ঘরের থেকে সাধারণ সৈনিকদের ওপর আসা চাপ কমাতে মুখ শাসকবর্গ কয়েকটা মামুলী সতর্কবাণী উচ্চারণ করা ছাড়া আর কিছুই করেনি। বাড়ির থেকে সেন্টিমেন্টাল বৌ-দের লেখা চিঠির মাধ্যমে বয়ে আনা বিষ সমস্ত সীমান্তটাকে বিষাক্ত করে তোলে। একবারও তারা ভাবেনি যে এর দ্বারা শত্রুপক্ষের জয়ের পথই প্রশস্ত করা হচ্ছে বা তাদের নিজেদের পুরুষদের কাজ প্রলম্বিত এবং দিনে দিনে কষ্টকর হয়ে উঠছে। জার্মান দ্রমহিলাদের লেখা এসব বোকা চিঠিগুলোর মূল্য শয়ে শয়ে বা হাজারে হাজারে প্রাণের বিনিময়ে দিতে হয়।
এভাবে ১৯১৬ সালে বেশ কিছু হতভাগ্যজনক ঘটনাবলীর প্রকাশ পায়। সমস্ত সীমান্তটাই গোমরাতে থাকে, অনেক বিষয়েই অসন্তোষে ফেটে পড়ে,–যার বেশিরভাগই ন্যায় ছিল। একদিকে যখন এরা ক্ষুধার্ত এবং রোগগ্রস্ত, বাড়িতে আত্মীয়স্বজন চরম দুর্দশায় দিন কাটাচ্ছে, ঠিক তখন অপর একদল মহোৎসব এবং পানোৎসবে মত্ত। হ্যাঁ, এমন কি সীমান্তের অবস্থাও একই প্রকার। যা হওয়াটা কোন রকমেই উচিত হয়নি।
এমন কি যুদ্ধের প্রারম্ভেই সৈনিকদের মধ্যে অসন্তোষের প্রবণতা ছিল; কিন্তু সমালোচনার ধোয়াটা নিজেদের ভেতরের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ থাকায় তা আর বাইরে প্রকাশের সুযোগ পায়নি। যে এ মুহূর্তে বন্য মোরগের মত বিড় বিড় করে অসন্তোষ প্রকাশ করত, সে-ই মুহূর্ত কয়েক পরে সেই অসন্তোষ চাপা দিয়ে নিচুপে তার কর্তব্যের জায়গায় ফিরে যেত; যেন সবকিছুই স্বাভাবিকভাবে চলছে। যে সৈন্যদল কিছুক্ষণ আগে অসন্তোষে ফেটে পড়েছে, পরের মুহূর্তে সে পরিখায় বসে দাঁত মুখ কামড়ে আক্রমণ চালিয়েছে, যেন জার্মানির ভাগ্য কয়েক শ’গজ কর্দমাক্ত এবং বোমাবিধ্বস্ত মাটির উপরেই নির্ভর করছে। গৌরবোজ্জ্বল সেই পুরনো সৈন্যদল তখনো পরিখা আঁকড়ে পড়ে আছে। আমার নিজের ভাগ্যের হঠাৎ পরিবর্তন আমাকে এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করায় যে সেখান থেকে আমি এ পুরনো সৈন্যদল এবং সদ্য বাড়ি থেকে আসা সৈনিকদলের পার্থক্য বুঝতে পারি। ১৯১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষাশেষি আমি যে সৈন্যদলে ছিলাম, সে দলটাকে শেষে যুদ্ধের জন্য পাঠানো হয়। আমাদের কাছে এটাই ছিল সত্যিকাবের রীতিমত ভারী যুদ্ধ— যেখানে দাঁড়িয়ে আমাদের এ ধারণাই হয় যে, এটাকে যুদ্ধক্ষেত্র বলে প্রকৃত নরক আখ্যা দেওয়াটাই সঠিক।
যদিও সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে অবিরত বোমাবর্ষণের মুখে আমরা স্থির অচঞ্চলভাবে দাঁড়িয়ে থাকি, এ বোমাবর্ষণের ফলে সামান্য যেটুকু জায়গা আমাদের বাধ্য হয়ে পরিত্যাগ করে পিছু হটতে হয়েছে, পরেই আবার দখলও নিয়েছি; যা আর কখনো তাদের আওতায় যায়নি। ১৯১৬ সালের ৭ অক্টোবর আমি আহত হই এবং নেহাত ভাগ্যের জোরে নিজেদের শিবিরে সে আহত অবস্থায় ফিরে আসতে পারি। আমাকে সাহায্যকারী ট্রেনে জার্মানিতে ফেরত পাঠাবার আদেশ আসে।
প্রায় দু’বছর হয়ে গেল আমি বাড়ি ছেড়ে এসেছি; এ পরিবেশে মাত্র দু’টো বছরকে অনন্তকাল বলে মনে হয়। আমি চেষ্টা করেও স্মৃতিতে আনতে পারি না জার্মান লোকেরা সৈনিকের পোশাক ছাড়া দেখতে কি রকম। হারমিসের হাসপাতালে এসে কর্মরতা এক নার্সের গলার স্বর শুনে আমি চমকে উঠি, সে আমার কাছে শুয়ে থাকা একজন আহতের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল। দু’বছর! এ সুদীর্ঘ দুবছর পরে জার্মান মেয়ের গলার স্বর শুনতে পেলাম।
সেই রিলিফ ট্রেন যত জার্মান সীমান্তের নিকটবর্তী হতে থাকে, তত বেশি চাঞ্চল্য জেগে ওঠে আমাদের ভেতরে। যে পথ ধরে দু’বছর আগে একজন যুবক কর্মী হিসেবে গেছি, সে পথগুলো যেন আমাদের কাছে অতি চেনা–ব্রাসেলস, লোভেন, লিগে; এবং শেষ পর্যন্ত আমরা যেন আমাদের জার্মান ভূমি চিনতে পারি।
১৯১৪ সালের অক্টোবর মাসে আমাদের হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল যখন আমরা এ সীমান্তকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাই। বর্তমানে নৈঃশব্দতা এবং সুগভীর আবেগ মনের ভেতরে সবচেয়ে বেশি মাথা উঁচু করে আছে। প্রত্যেকেই তার নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ জানায় কারণ যে ভূখণ্ডের জন্যে আমরা প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিলাম, সে ভূখণ্ড আবার আমরা দেখতে পেয়েছি এবং প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেকের দিকে লজ্জায় তাকাতে পারছিলাম না। সীমান্তে যুদ্ধে যাওয়ার প্রায় দ্বিতীয় বার্ষিকীতে আমি বার্লিনের কাছে চীলিৎসের হাসপাতালে ভর্তি হই।
কি বিরাট পরিবর্তন! সোমের কদমার্ত যুদ্ধক্ষেত্রের থেকে এ ধরনের বাড়ির ধবধবে সাদা বিছানায়। এ বাড়িতে ঢোকার সময়ে প্রত্যেকেরই দ্বিধা আসে। একমাত্র ধীরে ধীরে সবাই এ নতুন পৃথিবীতে আবার অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। দুর্ভাগ্যবশত সেখানে আরো কতকগুলো বিষয় ছিল যার জন্য এ নতুন জগত আমাদের অতি পরিচিত জগতের থেকে কিছুটা আলাদা ঠেকেছিল।
সীমান্তে সৈনিকদের সে উৎসাহ এখানে একান্তভাবেই অনুপস্থিত। আমিই প্রথম এমন কতগুলো বিষয়ের বিরোধিতা করি যা সীমান্তে কারোর এতদিন জানা ছিল না। বিশেষ করে নিজের কাপুরুষত্ব নিয়ে অহংকার করা। যদিও সীমান্তে অভাব অভিযোগের খামতি ছিল না, তবু আন্দোলন এবং এ অবাধ্যতা ও কাপুরুষতাকে অন্যের কাছে বিরাটভাবে তুলে ধরার প্রচেষ্টাও ছিল না। না, সীমান্তে একজন কাপুরুষ কাপুরুষই ছিল, তার বেশি কিছু নয়। বিশেষ করে তার ভয়টাই অন্যের ভেতরে সংক্রমিত হত। যেমন নায়কোচিত কারোর কাজকর্ম তাকে ঘিরে সবার প্রশংসা কাড়ত। কিন্তু এখানে, এ হাসপাতালে পুরো ব্যাপারটাই অন্যরকমের। গলা উঁচু আন্দোলনকারীরা সত্যিকারের ভাল সৈনিকদের নিয়ে ঠাট্টা পরিহাস করত এবং দুর্বল হাঁটু বিশিষ্ট কাপুরুষদের গৌরবের ঢঙে রাঙানোই ছিল এদের কাজ। কয়েকটা বিচিত্র মানুষ ছিল এ নিন্দুক দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা। তাদের মধ্যে একজন তো হাসপাতালে আমার জন্য চালাকি করে কিভাবে কাটা তারে নিজের হাত কেটেছে তার বর্ণনা দিতেই ব্যস্ত। যদিও তার ক্ষত অত্যন্ত সামান্য, কিন্তু তার ধরন-ধারণে মনে হচ্ছিল সে এখানে দীর্ঘদিন ধরেই আছে এবং অনন্তকাল ধরেই থাকবে। কোনরকম শঠতার দ্বারা নিশ্চয়ই এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ সর্বনাশাত্মক উদাহরণের ধৃষ্টতা এত প্রচণ্ড রকমের ছিল যে তার অসাধুতাকে সে সাহসের অভিব্যক্তি বলে বর্ণনা দিত যা নাকী সেই সাহসী সৈনিক যে মৃত্যুবরণ করেছে তার চেয়েও অনেক উঁচু। অনেকেই এসব কথাবার্তা চুপচাপ শুনত, কিন্তু বেশিরভাগই তার কথায় সায় দিত।
ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে এটা অসহ্য যে, এ রকমের রাজদ্রোহাত্মক একজন আন্দোলনকারীকে এ ধরনের একটা প্রতিষ্ঠানে থাকতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কি করার আছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও নিশ্চয়ই জানে লোকটা কে? সত্যি কথা বলতে কি, তারা জানত। তবু এ বিষয়ে তারা কিছু করেনি।
যেমাত্ৰ চলাফেরা করতে সক্ষম হই, আমি বার্লিন বেড়াবার জন্য ছুটি মঞ্জুর করাই।
সর্বত্র তিক্ত চাহিদার ছাপ। লক্ষ লক্ষ কাপুরুষে ভর্তি শহরগুলো অনাহারে কারাচ্ছে। বিভিন্ন হোটেলে, বিশ্রামাগারে একই ধরনের আলোচনা–যা আমাদের হাসপাতালে চলছে। দেখে শুনে আমার এ ধারণাই হয় যে আন্দোলনকারীরা ইচ্ছে করেই এককভাবে এসব জায়গায় জড়িয়ে পড়েছে যাতে তাদের মতামতটাকে সবার সামনে তুলে ধরা সম্ভব হয়।
কিন্তু মিউনিকের অবস্থা এর চেয়েও অনেক বেশি খারাপ। আমাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার পর সেখানকার সংরক্ষিত সৈন্যবাহিনীতে পাঠানো হয়। আমার চোখে মিউনিককে যেন অচেনা অজানা একটা শহর বলে মনে হয়। যেখানে যাওয়া যায় সে একই অভিযোগ। অসন্তোষ আর ক্রোধ। এরজন্য অবশ্য কিছু পরিমাণে দায়ী হল অসামরিক অফিসাররা। তারা অপটু অনভিজ্ঞ হাতে সৈন্যদের সঙ্গে ব্যবহার করেছে। তারা কোনদিন যুদ্ধক্ষেত্র দেখেনি এবং সে কারণেই যথাযোগ্যভাবে পুরনো সৈন্যদের সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় তা তাদের জানা ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই এসব পুরনো সৈন্যদের মধ্যে চারিত্রিক দিক থেকে নির্দিষ্ট কিছু জিনিস উপস্থিত হয়, যা তারা পরিখার মধ্যে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পেয়েছিল। এ সংরক্ষিত বাহিনীর পদস্থ কর্মচারীদের পক্ষে তা উপলব্ধি করা সম্ভব ছিল না, অথচ যারা যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়মিত সৈন্যদের সঙ্গে থেকেছে তারা তা বুঝতে পারত; সুতরাং সেই কারণে সে অনেক বেশি সম্মান পেত। এ যোগ্যতা থেকে সংরক্ষিত বাহিনীর অসামরিক পদস্থ কর্মচারীরা বঞ্চিত।
সীমান্তের কর্মরত উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা এ ব্যাপারটাকে বুঝতে পারলেও সংরক্ষিত বাহিনীর কর্মচারীরা ঠিক ব্যাপারটাকে অনুধাবন করে উঠতে পারত না। সুতরাং সাধারণ সৈনিকদের আচারে এ পাথর্ক তাদের চাখে বিরাট হয়ে ধরা দিত। কিন্তু এসব ছাড়াও সাধারণভাবে উৎসাহ বলতে কিছু ছিল না। এক কথায় শোচনীয় অবস্থা। এড়িয়ে যাওয়ার কলাকৌশলটাকেই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ বলে ভাবা হত; আর কাজের প্রতি একাগ্রতা ওদের ভাষায় দুর্বলতা বা গোঁড়ামী ছাড়া কিছু নয়। সরকারি অফিসগুলো ইহুদী কর্মচারীতে ঠাসা ছিল। কমবেশী প্রতিটি কেরানী ইহুদী এবং বলতে গেলে প্রতিটি ইহুদীই ছিল কেরানী। আমি এ বিরাট পছন্দ করা গোষ্ঠী দেখে অবাক হয়ে যেতাম, প্রকৃত সৈনিকদের মধ্যে যাদের উপস্থিতি নেহাত নগণ্য।
ব্যবসায় জগতের অবস্থা আরো ভয়াবহ। এখানে এককথায় ইহুদীদের ওপর পুরো দেশটা প্রচণ্ড রকমের নির্ভরশীল। জোকের মত তারা জাতির শরীর থেকে ধীরে ধীরে রক্ত শুষে নিচ্ছে। যুদ্ধের সময় সুসংগঠিত কোম্পানিগুলোর মাধ্যমে সমস্ত রকমের জাতীয় ব্যবসার দম বন্ধ করা অবস্থা। যাতে কোনরকম ব্যবসাই মুক্তভাবে না করা যায়।
সব কিছুকে কেন্দ্রীভূত করার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দেয়। সুতরাং ১৯১৬-১৭ সালের প্রথম ভাগে বাস্তবিকপক্ষে সমস্ত উৎপাদন ইহুদীদের অর্থনীতির কুক্ষিগত ছিল।
তবে কার বিরুদ্ধে জনসাধারণের এ ক্রোধ? আমি যেন মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছিলাম যে সেদিন সমাগত, যা আকস্মিক বিপদ ডেকে আনবে। যদি না সময় মত এর বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থা নেওয়া না হয়।
যখন ইহুদীরা সমস্ত জাতিকে বিনষ্ট করতে উদ্যত, গুদামঘরের চাবি পকেটে পুরেছে; প্রশিয়ানদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভে ইন্ধন জোগাচ্ছে; এবং সীমান্তে এ বিষাক্ত প্রচারকার্যের বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে না; এমন কি দেশের ভেতরেও তার প্রতিরোধের কোন ব্যবস্থা নেই। কেউ-ই তখনো বুঝতে সক্ষম নয় যে প্রুশিয়ার ধ্বংস ব্যাভেরিয়ার মুক্তি বা উন্নতি এনে দিতে পারে না। উপরন্তু, একের ধ্বংস অপরকেও সেখানে টেনে নামাবে।
এসব ব্যাপারগুলো আমাকে গভীরভাবে আঘাত করেছিল। কারণ এতে সেই ইহুদীদের চালাকি, জনসাধারণের চিন্তাধারার খাতটাকে তাদের ওপর থেকে অন্যদিকে বইয়ে দেবার প্রয়াস। যখন প্রশিয়ান আর ব্যাভেরিয়ানরা সামান্য বিষয় নিয়ে পরস্পর ঝগড়া বিবাদে রত, ইহুদীরা সে সুযোগে চোখের সামনে দিয়েই তাদের উপজীবিকা ছিনিয়ে নেয়। প্রশিয়ানরা যখন ব্যাভেরিয়ানদের গালাগাল দিতে রত, ঠিক তখনই ইহুদীরা এক সাজানো বিপ্লব বাধিয়ে দিয়ে প্রুশিয়া আর ব্যাভেরিয়া দুটোকেই একসঙ্গে ধ্বংস করে।
একই জার্মান জাতির মধ্যে পরস্পরের এ সামান্য বিষয় নিয়ে এ ঘৃণিত ঝগড়া আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারি না; যার থেকে আমার মনে হয় সীমান্তে ফিরে যাওয়াটাই ভাল। সে কারণে মিউনিক পৌঁছেই আমি চাকরিতে যোগ দেই। ১৯১৭ সালের মার্চের গোড়ার দিকে আমি সীমান্তে আমার পুরনো সৈন্য বাহিনীতে যোগদান করি।
১৯১৭ সালের শেষাশেষি আমার মনে হয় যেন সীমান্তে আমার হতাশার দিনগুলোকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। রাশিয়ার ধ্বংসের পর আমাদের সৈন্যবাহিনী তাদের আশা এবং সাহস ফিরে পায়। সবার একই ধারণা হয় যে যুদ্ধ আমাদের স্বপক্ষেই শেষ হবে। আমরা যেন আবার গলা ছেড়ে গান গাইতে পারব। দাঁড়কাকগুলো তাদের কর্কশ চিৎকার বন্ধ করেছে। পিতৃভূমির ভবিষ্যতের প্রতি আশা আবার প্রবল হয়ে ওঠে।
১৯১৭ সালের শরৎকালে ইতালিয়ানদের ধ্বংসের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত চমৎকার হয়। কারণ এ বিজয় এটাই প্রমাণ করে যে রাশিয়া ছাড়াও অন্য সীমান্ত তছনছ করে দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের আছে। এ উৎসাহজনক চিন্তাই সীমান্তের লক্ষ লক্ষ লোকের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং তারা উৎসাহের সঙ্গে ১৯১৮ সালের বসন্তকালের দিকে তাকিয়ে থাকে। কারণ তখন শত্রুরা যে চরম হতাশায় ভুগছে এ সত্যটা প্রকট হয়ে পড়েছে। শীতকালে সীমান্তটা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি শান্তরূপ ধারণ করে। কিন্তু তা হল ঝড়ের আগের শান্ত অবস্থা, স্তব্ধতা।
ঠিক যখন শেষ আত্মরক্ষার প্রচণ্ড রকমের প্রস্তুতি চলেছে, যা কিনা এ যুদ্ধের শেষ টেনে আনবে, যার জন্য অন্তহীন যানবাহনের সারী মানুষ আর গোলাবারুদ বয়ে আনছে সীমান্তে এবং সৈন্যরা শেষ ও প্রচণ্ড আক্রমণের জন্য তৈরি হচ্ছে, ঠিক তখনই এ যুদ্ধের সময়ে জার্মানি সাংঘাতিক রকমের এক বিশ্বাসঘাতকতার সম্মুখীন হয়।
জার্মানিকৈ কিছুতেই যুদ্ধে জিততে দেওয়া হবে না। ঠিক যে মুহূর্তে বিজয়লক্ষ্মী জার্মানির গলায় মালা পরাতে উদ্যত, তখনই এমন একটা ষড়যন্ত্র করা হয়; একটা প্রচণ্ড মুষ্ঠাঘাতে জার্মানিকে শয্যাশায়ী করে দিয়ে বিজয় থেকে তাকে অনেক দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। গোলাবারুদ এবং অস্ত্রশস্ত্রের কারখানায় পূর্ণ হরতালের ব্যবস্থা করা হয়।
এ ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্য যদি সফল হত তবে জার্মান সীমান্ত ধ্বংস হয়ে পড়ত এবং ভোরভার্ক অর্থাৎ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ইচ্ছে জার্মানি যেন কিছুতেই যুদ্ধে জিততে না পারে, পূর্ণ হত। গোলাবারুদের অভাবে কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সীমান্ত ভেঙে পড়ত, আত্মসংরক্ষণের কাজও থেমে যেত; এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রীভাব বজায় থাকত। তখন আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা জার্মানির অর্থনীতিকে পরিচালনা করার সুযোগ পেত–এর মূল উদ্দেশ্যই ছিল জাতীয় অর্থনীতি ব্যবস্থাকে ভেঙে দিয়ে আন্তর্জাতিক ধনতন্ত্র ব্যবস্থাকে তার জায়গায় কায়েম করা। এবং এ উদ্দেশ্য সত্যি বলতে কি পূর্ণও হয়ে যেত, তারজন্য একদিকের বিশ্বাস প্রবণতা আর অপরদিকের বিশ্বাসঘাতকতাকে ধন্যবাদ।
যাহোক বিস্ফোরক উৎপাদনের কারখানাগুলোর ধর্মঘট শেষপর্যন্ত যা আশা করা গিয়েছিল সেই সাফল্য আনতে পারেনি। বিশেষ করে সীমান্তে গোলাবারুদের অভাব সৃষ্টি করা। কারণ এ ধর্মঘট সৈন্যবাহিনীকে গোলা বারুদের অভাবে সামগ্রিক ধ্বংস ডেকে আনার পক্ষে অতি অল্পদিন ধরে চলেছিল, যা আগে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কিন্তু নৈতিক দিক থেকে প্রচণ্ডরকম ক্ষতি যে হয়েছিল তা অস্বীকার করার উপায় নেই।
প্রথমত দেশের লোক যদি জয় না চায়, তবে কিসের জন্য এ সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করে চলেছে? কার জন্য এ আত্মত্যাগ আর অসীম কষ্ট এরা সহ্য করছে? যখন দেশের ভেতরে লোকেরা ধর্মঘট করে হাত গুটিয়ে বসে থাকবে, তখনো কি সৈন্যরা যুদ্ধ করে যাবে?
১৯১৭–১৮ সালের শীতকালটা এ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রীর আকাশে কালো মেঘ ঝুলে রয়েছে। প্রায় চার বছর ধরে ক্রমাগত জার্মানির ওপরে আক্রমণের পর আক্রমণ চালানো হয়েছে, তবু তাদের পক্ষে জার্মানিকে মাটিতে শোওয়ানো সম্ভব হয়ে ওঠেনি। যে তাদের ঠেলে দূরে সরিয়ে রেখেছে, — এক হাতে তার নিজেকে রক্ষার নিমিত্ত ঢাল ধরা, অপর হাতে শক্রর সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য তরোয়াল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ শক্ররা এক সময় ধ্বংস হয়, এখন তার পশ্চিমের সঙ্গে যুদ্ধ চালাবার জন্য হাত মুক্ত। অবশ্য এ কাজের জন্য রক্তের নদী বয়ে গেছে; তবু তার দু’হাত এখন মুক্ত, সুতরাং এক হাতে ঢাল আর অপরহাতে অসি ধরে সে এখন পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধ চালাবার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত এবং যেহেতু শত্রুরা জার্মানির আত্মরক্ষণ ভেঙে তছনছ করতে পারেনি, তাই জার্মানিই এখন তাদের প্রতি আক্রমণ করতে শুরু করে। জার্মানির এ জয়ের সম্ভাবনার কাছে শত্রুরা ভয়ে কেঁপে ওঠে।
প্যারিস এবং লন্ডনে একের পর এক সম্মেলন শুরু হয়। এমন কি শত্রুদের প্রচারকার্যও প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। জার্মানির জয়ের আর কোন আশা নেই,–এ প্রচার চালানো আর আগের মত এত সহজ হয় না। একটা স্তব্ধতা সীমান্তে বিরাজ করে। এমন কি সেই স্তব্ধতা শুধু জার্মান সৈন্যদের মধ্যে নয়, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সৈনিকদের মধ্যেও তার ছায়া পড়ে। তাদের প্রভুদের প্রগলভতা হঠাৎ বন্ধ হয়। নেমে আসে বিরক্তিকর সত্যের সকাল। জার্মান সৈন্য সম্পর্কে তাদের ধ্যান-ধারণা ততদিনে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। বর্তমানে তাদের অভিমত হল, এ হল এমন এক ধরনের বোকা সমাপ্তি যার ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু বাস্তবে দেখে সে বোকারাই রাশিয়ানদের মৈত্রী ভেঙে এগিয়ে গেছে। পূর্বদিকের আত্মরক্ষণ নীতি, যা নাকি জার্মান সামরিক কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতির কারণে জারী করেছিল, এখন সেটাই অপরপক্ষের চোখে কলাকৌশল বলে ধরা দেয়। তিন বছর ধরে জার্মানরা রাশিয়ার সীমান্তে ঝোপঝাড় ঠেঙিয়ে চলেছে, কিন্তু লাভ বলতে কিছুই হয়নি। এ নিষ্ফল কাজকর্ম ফেলে সবাই মুখ সিটকেছে; কারণ তখন সকলেরই ধারণা ভবিষ্যতে কেবল সৈন্য সংখ্যার জোরেই রাশিয়া এ যুদ্ধে জিতে যাবে। রক্ত ঝরতে ঝরতে জার্মানি ক্ষয়ে যাবে। এবং ঘটনাবলীও এ আশাকেই সমর্থন করেছিল।
১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বরের দিনগুলোতে ট্যানেনবার্গের যুদ্ধের পর যখন প্রথম রাশিয়ার অনন্ত যুদ্ধবন্দীর সারি জার্মানির ভেতরে ঢোকে, তখন মনে হয়েছিল এর সম্ভবত আর শেষ নেই; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল একজন সৈনিক মারা গেলেই তার জায়গায় আরেকজন প্রস্তুত হয়ে রয়েছে। এ বিশাল সাম্রাজ্যের জারের কাছে এত বিশাল পরিমাণে সৈন্য মজুত যে মনে হয় এ সৈন্যবহিনী অক্ষয়; নতুন নতুন শুরু যেন সেই যুদ্ধ দলের হোতার কাছে সর্বদাই প্রস্তুত।
এ দীর্ঘ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জার্মানি আর কতক্ষণ বুঝতে পারবে? এখনো পর্যন্ত সেই চরম দিন এসে উপস্থিত হয়নি, যখন জার্মানি শেষ যুদ্ধে জয়ী হবে। কিন্তু তখনো তো সেই শেষ যুদ্ধের জন্য রাশিয়ার কাছে প্রচুর সৈন্য মজুত থাকবে। এবং তারপরে? মনুষ্যত্বের পরিমাপে জার্মানির ওপরে রাশিয়ার বিজয় হয়ত বা দেরি হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘদিন পরে হলেও তা আসবে।
রাশিয়াকে ঘিরে যে আশার জাল গড়ে উঠেছিল, তা এখন অন্তর্হিত। যে মৈত্রী এত প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষয় করেছে, তাদের পরস্পরের স্বার্থের ভাণ্ডার নিঃশেষিত। নির্দয় শত্রুর সামনে তারা ভূমিতে শয্যাগ্রহণ করেছে। ভয়বিহ্বলতা এবং হতাশা মৈত্রী রাষ্ট্রের সৈন্যদের মধ্যে তার থাবা প্রসারিত করেছে; এতদিন যারা একটা অন্ধ বিশ্বাসের মোহে আচ্ছন্ন ছিল, তারা এখন আগত বসন্তকে ভয় করছে। কারণ তারা বুঝেছে মাত্র কিছু পরিমাণে শক্তি পশ্চিমের সীমান্তে সংগঠিত করা সত্ত্বেও তারা জার্মানদের পরাজিত করতে পারেনি, সেক্ষেত্রে কী করে এ বিশাল সৈন্যসম্ভারকে পরাজিত করা সম্ভব যেখানে এ অবাক করা দেশের বীরবৃন্দ প্রচণ্ড আক্রমণের জন্য পশ্চিম সীমান্তে জড় হচ্ছে?
দক্ষিণ থেরোলের ঘটনাবলীর ছায়া যেন এখানে প্রতিফলিত। জেনারেল ক্যাডোনার প্রেতেরা যেন হঠাৎ এখানে এসে জড় হয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সৈন্যদের মুখে তার ছায়া সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। যুদ্ধ জয়ের আশার চেয়ে হেরে যাওয়ার আশঙ্কাটাই এখন প্রকট।
সে ঠাণ্ডায় রাত্রিগুলোতে, যখন প্রত্যেকেই প্রায় শুনতে পেত জার্মান সৈন্যদের এগিয়ে যাওয়ার প্রতিধ্বনি এবং কম্পিতবক্ষে অপেক্ষা করত সেই দিনটার জন্য, হঠাৎ যেন একটা চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলকানি জার্মানিতে জ্বলে ওঠে এবং তার রশিতে শত্রু সীমান্তের বোমা বর্ষণে বিধ্বস্ত জমিগুলোকে দেখিয়ে দেয়।
যখন জার্মান সৈন্যবাহিনী প্রচণ্ড রকমের আক্রমণ চালাবার আদেশ পেয়েছে, ঠিক তখনই জার্মানিতে সর্বাত্মক ধমর্ঘট হয়।
প্রথমে তা সারা পৃথিবী হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। সে হতবুদ্ধিকর অবস্থার ঘোর কাটলে শত্রুরা আবার প্রচারকার্যে কোমর বেঁধে নেমে পড়ে, এবং শেষ মুহূর্তে তাদের ওপর শিকারী বাজের মত ঝাপিয়ে পড়ে। হঠাৎ একটা উপায়ের রশ্মি নজরে আসে, যার দ্বারা বিভিন্ন রাষ্ট্রের সৈন্যদের ডুবে যাওয়া আত্মবিশ্বাস আবার খুঁজে পায়। জয়ের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, আগামী ঘটনাগুলোর সম্পর্কে অমঙ্গলের পূর্বাভাস এখন একটা দৃঢ় সঙ্কল্পের নিশ্চয়তায় ধরা দেয়। যে সব সৈন্যবাহিনীকে জার্মান আক্রমণের প্রচণ্ডতা সহ্য করতে হয়েছে, যে আক্রমণের প্রচণ্ডতা পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই দেখা গেছে, তারাই এখন শেষ বিচারের রায়ে উদ্দীপিত যে জার্মান ধৃষ্টতার জন্য নয়, বরং অপরপক্ষে আত্মরক্ষণের সহিষ্ণুতারই জয় অবশ্যম্ভাবী। এখন শুধু জার্মানদের তরফ থেকে বেছে নেওয়া কারা জয়ী হবে। কারণ পিতৃভূমিতে তারা বিপ্লব করতে ভালবাসে, জয়ী হতে নয়।
ব্রিটিশ, ফরাসী এবং আমেরিকান সংবাদপত্রগুলো এ বিশ্বাসটাই তাদের পাঠকদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় আর সুচারুরূপে এ প্রচার ব্যবস্থাকে হাজির করা হয় সীমান্তে, তাদের নিজ নিজ সৈন্যবাহিনীর সামনে।
জার্মানিতে বিপ্লব শুরু হয়েছে, সুতরাং মিত্রশক্তির জয় অনিবার্য! এটাই হল পাউল আর টমির আস্থা ফিরিয়ে এনে তাদের নিজেদের পায়ে দাঁড় করানোর সর্বশ্রেষ্ঠ ওষুধ। আমাদের রাইফেল এবং মেশিনগান আবার আগুন ঝরাতে শুরু করে; কিন্তু তা ভয় বিহ্বল শত্রুদের মধ্যে আশঙ্কার সৃষ্টি করে না।
গোলাবারুদের কারখানায় ধর্মঘটের এ হল ফলাফল। শক্র দেশগুলোতে জয়ের বিশ্বাস এভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যা ধীরে ধীরে তাদের হাত শক্ত করে এাং সঙ্গে সঙ্গে মিত্ররাষ্ট্রগুলোর হতাশার ভাবও কেটে যায়। এ ধর্মঘটের ফলে হাজার হাজার জার্মান সৈন্য প্রাণ হারায়। কিন্তু এ ঘৃণ্য কুকর্মের প্ররোচকরা যারা এ ভীরু ধর্মঘট সুসংবদ্ধ করেছিল, তারা ছিল এ বিপ্লবের হোতা।
প্রথমে অপ্রত্যক্ষভাবে মনে হয়েছিল জার্মান সৈন্যদের এসব ঘটনাবলীর প্রতিক্রিয়া তারা সহজেই কাটিয়ে উঠতে পারবে। এখানে প্রতিরোধের সময়ে শত্রুপক্ষের চারিত্রিক দিক থেকে সৈনিকদের সংঘর্ষশীল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যায়। তার জায়গায় স্থান নেয় যুদ্ধে জেতার এক ভয়ানক প্রতিজ্ঞা। কারণ মানুষের বিচারের মানদণ্ডে যদি পশ্চিম সীমান্তে জার্মান আক্রমণটাকে কয়েকটা মাস রোখা যায়, তবেই যুদ্ধে জয় অবশ্যম্ভাবী। মিত্রপক্ষের সংসদও এ উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত সমর্থন করে বিরাট একটা অঙ্ক প্রচারকার্যের জন্য ব্যয় অনুমোদন করে, যার উদ্দেশ্য ছিল জার্মানির আভ্যন্তরিক শক্তিকে ভেঙে টুকরো টুকরো করা।
এটা আমার ভাগ্যই বলতে হবে যে প্রথম দুটো এবং শেষবারের প্রচণ্ড আক্রমণে অংশগ্রহণ করতে পেরেছিলাম। এসব ঘটনাবলী আমার জীবনে প্রচণ্ড বিস্ময়ের ছায়া ফেলে,–বিস্ময়কর। কারণ শেষবারের মত যুদ্ধ তার আত্মরক্ষণ নীতি ছেড়ে দিয়ে আক্রমণাত্মক চরিত্র বেছে নেয়, ১৯১৪ সালে যা করা হয়েছিল। জার্মান সৈন্যদের পরিখার বুক থেকে আশ্বাসের নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে এবং তিন বছরের দীর্ঘ ধৈর্যের পরে তারা যেন ডোভায় চড়ে নরকে উপস্থিত হয়; হিসেব চুকোবার দিন সমাগত। আবার সেই কামলিন্দু বিজয়োৎসবের জয়ধ্বনি বিজয়ী সৈন্যদের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে। জয়কে তারা অমর সম্মানের সঙ্গে কণ্ঠলগ্না করতে শেষ পর্যন্ত সমর্থ হয়েছে। আবার সেই দেশপ্রেমের সঙ্গীতগুলো সরবে গাওয়া শুরু হয়, এ যেন তাদের অন্তহীন স্বর্গের দিকের রাস্তা, এবং শেষবারের মত ঈশ্বর তার অকৃতজ্ঞ সন্তানদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি হাসে।
১৯১৮ সালের গ্রীষ্মের মাঝামাঝি, গুমোট একটা আবহাওয়া যেন সীমান্তকে ঘিরে ধরে। দেশের অভ্যন্তরে তখন পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া চলছে। কিন্তু কী নিয়ে? আমরা যতটুকু শুনতে পেরেছি তাতে মনে হয় সীমান্তের বিভিন্ন সৈন্যদলের রকমারী বিষয়ে ঘিরে এ ঝগড়া দানা বেঁধে উঠেছে, যুদ্ধটা একটা হাসির ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে। একমাত্র হঠকারী লোকেরাই এখনো জয়ের আশা রাখে। এ যুদ্ধ চালিয়ে যাবার স্বপক্ষে এখন আর জনতা নেই; একমাত্র পুঁজিবাদ এবং সম্রাটই তাদের নিজেদের স্বার্থে এটাকে বয়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছুক। এ ধরনের চিন্তাধারাই দেশের অভ্যন্তর থেকে সীমান্তে ভেসে আসত আর আলোড়িত হত।
.
প্রথম প্রথম এ গুজব সামান্যই হয়েছিল। সার্বজনীন মত প্রকাশের মূল্য আমাদের কাছে কতটুকু? এর জন্যেই কি গত চার বছর ধরে আমরা যুদ্ধ করে চলেছি? এটা হল আমাদের বীরদের কবর থেকে ভীরুর মত অপহরণ করা, যে মহৎ কারণে তারা আজ ভূমিশয্যায় শায়িত, তার দাম আর কতটুকু! আমাদের সৈন্যরা ফ্লানডার্সে শ্লোগান তুলেছিল যে ‘সাবর্জনীন মতপ্রকাশ চিরজীবী হোক’–তারা আবার নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। কিন্তু ক্রন্দিত সুরে গেয়ে ওঠে, পৃথিবীতে জার্মানি হল সকলের ওপর। নিচু স্বর হলেও উল্লেখযোগ্য তেমন কোন পরিবর্তন ছিল না। সংখ্যাগরিষ্ঠ যারা এ সার্বজনীন মত প্রকাশের জন্য চিৎকার করছিল, যখন এরা যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়ায়, তারা কিন্তু তখন এতে অনুপস্থিত। এ সব রাজনৈতিক ইতর প্রাণীগুলো সীমান্তে আমাদের কাছে একেবারেই অপরিচিত। সে দিনগুলোতে যেখানে দলে দলে সৎ জার্মানদের জমায়েত, সে জমায়েত এ তথাকথিত ভদ্রসম্প্রদায় থেকে আসা মুষ্টিমেয় সংসদ সদস্যদের দেখা মিলত।
পুরনো সৈন্যদল যারা সীমান্তে যুদ্ধরত, তারা এ নতুন অস্ত্রসম্ভার যা মেসার্স অ্যাবাটি, সাইডম্যান, ব্যর্থ, লীভলেক্ট এবং অন্যান্যদের কাছ থেকে আসত, একেবারেই পছন্দ করত না। আমরা বুঝতে পারতাম না কেন? হঠাৎ এসব কর্তব্যে পরাসুখ ব্যক্তিরা সমস্ত শাসন ক্ষমতাকে নিজের বলে অন্যায় দাবি জানাতে তৎপর হয়ে ওঠে—–যাদের সৈনিকদের প্রতি বিন্দুমাত্র আস্থা নেই।
গোড়া থেকেই আমার নিজের ব্যক্তিগত মতামত স্থির ছিল। আমি অন্যের থেকে বেশি এ রাজনৈতিক নেতাদের চক্রকে অনুসরণ করে এসেছি; যারা বারবার বিশ্বাসঘাতকতা করে এসেছে। আমি অনেক আগেই উপলব্ধি করেছি যে এ কুখ্যাত নাবিকদের কাছে জাতির স্বার্থের ভূমিকা অতিশয় নগণ্য। তারা তাদের নিজেদের পকেট ভর্তি করার ধান্ধাতেই এসব কাজকর্ম করে চলেছে। আমার অভিমত হল, সোজা এদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। কারণ তারা শান্তিকেই বলি দিতে উদ্যত, এবং প্রয়োজন বোধে ষড়যন্ত্র করে জার্মানিকে পরাজিত করতেও এদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই; অবশ্যই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। তাদের ইচ্ছাপূরণ করার অর্থ হল শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থকে একদল চোরের স্বার্থের বিনিময়ে জলাঞ্জলী দেওয়া। তাদের ইচ্ছাকে সমর্থন জানানোর মানে হল জার্মানিকে উৎসর্গ করা।
সৈন্যদলের গরিষ্ঠভাগ এ মতামতই পোষণ করত। কিন্তু নতুন সৈন্য যা বদলী হিসেবে দেশ থেকে আসছে তা দ্রুতগতিতে নিকৃষ্ট থেকে নিকৃষ্টতর হতে থাকে। ব্যাপারটা এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়ায়, যখন এ নতুন সৈন্যদের আগমন দলের শক্তিবৃদ্ধি করা দূরে থাকুক, যুদ্ধ করার ক্ষমতাটাকেই কমিয়ে দিতে থাকে। নতুন সগ্রহ করা যুবক সৈন্যদের বেশিরভাগই হল অপদার্থ। অনেক সময়ে এটা বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে যে তারা এ একই জাতির সন্তান-যারা ইব্রিস্ ঘিরে রক্তক্ষয়ী সগ্রামে একদিন মেতেছিল।
আগস্ট সেপ্টেম্বরে এ নৈতিকতার মূল্য আরো বেশি দ্রুতগতিতে নিম্নগামী হয়। যদিও শত্রুপক্ষের আক্রমণ আমাদের আগেকার আত্মরক্ষণমূলক যুদ্ধের সঙ্গে কোনরকম তুলনাই চলে না। এ আক্রমণের তুলনায় লোমের এবং ফ্লান্ডার্সের বীভৎস যুদ্ধের ছবি এখনো আমাদের স্মৃতিতে জেগে রয়েছে।
সেপ্টেম্বরের শেষে আমরা তৃতীয়বার সে জায়গাগুলো দখল করি। যা আমরা যখন নতুন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে সেনাবাহিনীতে ঢুকেছিলাম, তখন ঝটিকাগতিতে দখল করেছিলাম। কী সুন্দর স্মৃতি!
এখানেই আমাদের যুদ্ধ হয়; সেটা হল ১৯১৪ সালের অক্টোবর এবং নভেম্বর মাস। হৃদয়ে দেশের প্রতি প্রজ্জ্বলিত ভালবাসা এবং কণ্ঠে গান নিয়ে আমাদের তরুণ সেনাদল এগিয়ে চলে দুর্বার গতিতে। যেন তারা নাচের আসরে যোগ দিতে চলেছে। রক্তের ধারা এ ধারণাতেই তারা ঢেলে দেয় যে তা পিতৃভূমির স্বাধীনতারক্ষার এবং অর্জনের কাজে লাগছে।
১৯১৭ সালে দ্বিতীয়বারের মত সেখানে পদার্পণ করি, যেটাকে আমরা পবিত্রভূমি বলে এতদিন গণ্য করে এসেছি। এখানেই সেইসব শ্রেষ্ঠ সহকর্মীরা শায়িত, বয়সের দিক থেকে যারা মাত্র বালক অবস্থা পেরিয়ে এসেছে, সেইসব সৈন্য যারা উজ্জ্বল চোখে বুকভরা দেশপ্রেম নিয়ে মৃত্যুর দিকে ধেয়ে গেছে।
আমাদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ, সে সৈন্যদলে গোড়ার থেকেই ছিল। আবেগে আপুত হয়ে পড়ি সেই পবিত্রভূমিতে দাঁড়িয়ে, যেখানে দাঁড়িয়ে একদিন আমরা শপথ নিয়েছিলাম যে মৃত্যু পর্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে কর্তব্যে অবিচল থাকব। তিন বছর আগে সৈন্যদল ঝটিকা গতিতে আক্রমণ করে এ জায়গাটা দখল করেছিল। এখন আবার তাদের ডাক পড়েছে নির্দয় সংঘর্ষের মুখে এটাকে রক্ষা করার।
কিন্তু সপ্তাহ ধরে পদাতিক বাহিনীর বোমা বর্ষণের সাহায্যে ইংরেজ ফ্লান্ডার্সে তাদের আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে গড়ে তোলে। মনে হয় যেন মৃত আত্মাগুলো আবার জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সেনাবাহিনী কাদার তলায় ডুবতে থাকে। বোমার আঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন তবু পালানো বা ভয় পাওয়ার কোন চিহ্ন তাদের মধ্যে নেই। শুধু দিনের পর দিন তারা সংখ্যায় কমে যেতে থাকে। অবশেষে বৃটিশ তাদের আক্রমণ শুরু করে ৩১শে জুলাই, ১৯১৭ সালে।
আগস্টের শুরুতে আমাদের ছেড়ে দেওয়া হয়, পুরো সৈন্যবাহিনী তখন কমতে কমতে কয়েকটা দলে এসে ঠেকেছে মাত্র, যারা তখনো কাদা কামড়ে পড়ে রয়েছে, তাদের অবস্থা ভূত প্রেতের মত। মানুষ বলে চেনা যায় না।
১৯১৮ সালের শঙ্কালে আমরা তৃতীয় বারের মত সেই ভূমির ওপরে এসে দাঁড়ালাম, যা আমরা ঝড়ের গতিতে ১৯১৪ সালে দখল করেছিলাম। কোমিনস্ গ্রাম; যেটা আগে আমাদের যুদ্ধের পটভূমি হিসেবে কাজ করেছে, এখন সেটাই হয়ে দাঁড়ায় রণক্ষেত্র। যদিও সে গ্রামের চারিদিকের প্রবর্তন অতি নগণ্যই হয়েছে, তবু মানুষগুলো যেন বদলে গেছে একবারেই। এখন তারা রাজনীতি চর্চা করে। সব জায়গার মত এখানেও দেশের ভেতরকার হাওয়া এসে বিষ ছড়িয়েছে। যুবকরা তো এতে পুরোপুরি ডুবেছে। কারণ তারা এখানে এসেছে সোজা দেশ থেকে।
অক্টোবর ১৩-১৪ই রাতে বৃটিশরা ইউসের দক্ষিণ সীমান্তে গ্যাসের সাহায্যে আক্রমণ শুরু করে। তারা হলদে গ্যাস ব্যবহার করেছিল যা আমাদের কাছে নিতান্তই অজানা, অন্ততপক্ষে এ বিষয়ে আমাদের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। আমার ভাগ্যই যেন সেই রাত্রে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের নিমিত্ত নির্দিষ্ট ছিল। ভারভিক্রের দক্ষিণে একটা পাহাড়ের মাথায়, ১৩ই অক্টোবরের সন্ধ্যায়, আমরা গ্যাস বোমার আঘাতে প্রচণ্ড রকমের বিপর্যস্ত হই। প্রায় সারাটা রাত ধরেই এক নাগাড়ে এ বোমাবর্ষণ চলেছিল। মাঝ রাত বরাবর আমাদের মধ্যে বেশ ক’জন মাটিতে লাফিয়ে পড়ে; কিছু আহত, বাকিরা চিরদিনের জন্য ভূমিতে শুয়ে পড়ে। সকালের দিকে আমিও চোখে ব্যথা অনুভব করি। প্রতি পনের মিনিটে ব্যথাটা যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। এবং সকাল সাতটার সময় আমার চোখে ভয়ঙ্কর জ্বালা ধরে যখন আমি শেষবারের মত পেছনে ঝুঁকে শেষ গুলিটা শত্রুর দিকে ছুঁড়ি। আমার ভাগ্যই আমাকে এ যুদ্ধে টেনে এনেছে। কয়েক ঘন্টা পরে আমার চোখ দুটো যেন জ্বলন্ত কয়লার মত জ্বলতে থাকে, এবং চারিদিকের দৃশ্যমান সবকিছু আমার কাছে তখন অন্ধকার।
আমাকে পোমেরিনা পেস্ওয়াক হাসপাতালে পাঠানো হয়, যেখানে আমি প্রথম এ বিপ্লবের কথা শুনতে পাই।
দীর্ঘদিন ধরেই হাওয়ায় কিছু ভাসছিল, যা ঠিক স্পষ্ট নয়, কিন্তু অপ্রীতিকর। লোকেরা তখন কানাকানি শুরু করেছে যে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কিছু একটা ঘটতে চলেছে, যদিও আমি কল্পনাতে আনতে পারিনি যে ব্যাপারটা সঠিক কিনা। প্রথমে ভেবেছি গত বসন্তের মত কোন ধর্মঘট হয়ত বা ঘটতে যাচ্ছে। নৌ-বাহিনী থেকে ক্রমাগত অপ্রীতিকর গুজব আসছে, যা নাকি তখন ফুলে ফেঁপে বিস্ফোরিত অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু আমার যেন মনে হল পুরো ঘটনাটাই কয়েকটা নিঃসঙ্গ যুবকের প্রমোদের ব্যাপার। এটা সত্যি যে হাসপাতালে সবাই এ যুদ্ধের সমাপ্তি নিয়ে কথাবার্তা বলছে, এবং তারা আশা করছে যে সেটা খুব বেশি একটা দূরের নয়। কিন্তু কেউ-ই বোধহয় আশা করেনি যে এত তাড়াতাড়ি ফয়সালা হয়ে যাবে। আমার পক্ষে তখন সংবাদপত্র পড়া সম্ভব নয়।
নভেম্বরে সেই উদ্বিগ্নতা আরো বৃদ্ধি পায়। এবং একদিন আমাদের ওপর সর্বনাশা বিধ্বংস নেমে আসে; হ্যাঁ, কোনরকম সতর্কতা ছাড়াই। নাবিকেরা মোটর লরীতে ভর্তি হয়ে এসে আমাদের বিদ্রোহ করার জন্য প্ররোচিত করতে থাকে। আমাদের জাতির সেই ‘স্বাধীনতা, সুন্দর এবং আত্মমর্যাদার’ যুদ্ধে কয়েকটা ইহুদী ছেলে সে দলের নেতা। এদের মধ্যে একটাকেও সীমান্তে কর্মরত অবস্থায় দেখা যায়নি। হাসপাতালের মাধ্যমে যৌন ব্যধিগ্রস্ত বলে পূর্বদেশীয় এ তিনজনকে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে তাদের হেঁড়া লাল কাপড়ের টুকরোটাকে পতাকা হিসেবে তারা উড়াচ্ছে।
কয়েকদিন পরে আগের থেকে অনেক সুস্থ বোধ করি। চোখের গোলকে সেই আগেকার ব্যথাটা কমে আসে। ক্রমে ক্রমে আমাকে ঘিরে থাকা চারিদিকের পরিবেশগুলোর উপর থেকে ঝাঁপসা ভাবটা সরে যায়। এখন আমি তাদের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম। কিন্তু আবার কোন নক্সা প্রস্তুত করতে পারব এ জীবনে এটা আমি আশাই করতে পারিনি। যাহোক প্রয়োজনের ঘণ্টা যখন উপস্থিত, তখন আমি আরোগ্যের পথে চলেছি।
আমার প্রথমে ধারণা হয়েছিল যে এ প্রচণ্ড রকমের উদ্বিগ্নতা সাময়িক ব্যাপার। আমি এ ধারণাটা আমার সহকর্মীদের ভেতরেও ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি। বিশেষ করে হাসপাতালে আমার ব্যাভেরিয়ার সহকর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে এতে সায় দিয়েছে। সব কিছু ছেড়ে দিয়ে তাদের ঝোক কিন্তু বিপ্লবের দিকে। আমি কল্পনাতেও আনতে পারি না যে মিউনিকও এ পাগলামীতে মেতে উঠেছে। কারণ আমার ধারণায় ভিটেবায়ের প্রতি বিশ্বস্ততা কয়েকটা ইহুদীর ইচ্ছা থেকে অনেক বেশি। সুতরাং আমি ভাবতেই পারি না
এটা নিছকই ‘নৌ-বিদ্রোহ’ এবং কয়েকদিনের মধ্যেই এটা চাপা পড়ে যাবে।
অল্প কিছুদিনের মধ্যে আমি জীবনের সবচেয়ে স্তম্ভিত করা খবর পেলাম। গুজবটা ক্রমাগত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। আমাকে বলা হয়, যে ব্যাপারটাকে আমি এতদিন স্থানীয় একটা ঘটনা বলে ভেবে এসেছি সেটা তা নয়। এটা হল সর্বাত্মক একটা বিপ্লব। এর সঙ্গে সীমান্ত থেকে এ সংবাদও আসে যে তারা আত্মসমর্পণ করতে ইচ্ছুক। এ জিনিস কি কখনো সম্ভব!
১০ই নভেম্বর স্থানীয় ধর্মযাজক হাসপাতাল পরিদর্শনে আসে, যার উদ্দেশ্য ছিল ছোটখাটো একটা বক্তৃতা দেওয়া; এবং এভাবেই আমরা পুরো ঘটনাটা জানতে পারি।
এ বক্তৃতা শোনার পর সঙ্গে সঙ্গে যেন জ্বরের মত আমার শরীরে শিহরণ খেলে যায়। সেই বৃদ্ধযাজক যেন আবেগে কাঁপছে, যখন সে আমাদের জানায় যে হোয়েন ঝোলায়েন আর রাজকীয় মুকুট পরবে না, কারণ পিতৃভূমি এখন গণতান্ত্রিক দেশ; আমরা সবাই যেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন এ নতুন ব্যবস্থার প্রতি তার আশীর্বাদ বর্ষণ করেন, এবং আগামী দিনগুলোয় দেশবাসীকে যেন পরিত্যাগ না করেন। সংবাদটা ঘোষণার সময়ে সে সংক্ষেপে রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানায়। পোমেরিনা থেকে প্রশিয়া পর্যন্ত। বলতে গেলে পিতৃভূমি জার্মানির প্রতি যেভাবে সে তার কর্তব্য করে গেছে, তার জন্য–এরপরেই সে কাঁদতে শুরু করে। সেই জায়গায় জমায়েত মানুষগুলোর ওপর একটা গভীর হতাশা নেমে আসে। আমার দৃঢ় ধারণা একটা চোখের অস্তিত্বও সেখানে ছিল না, যার থেকে অশ্রু না ঝরেছে। আমার কথা বলতে গেলে বলতে হয় আমি সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়েছিলাম, যখন সেই বৃদ্ধ ধর্মযাজক আবার বলতে শুরু করে যে আমাদের এ দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে এখন ছেদ টানা উচিত। কারণ এ যুদ্ধে আমরা হেরে গেছি, এবং আমরা বর্তমানে বিজয়ীর দয়ার ওপরে নির্ভরশীল। পিতৃভূমিকে এর জন্য ভবিষ্যতে অনেক বড় বোঝা বহন করতে হবে। আমাদের এখন যুদ্ধ বিরতির শর্তগুলোকে মেনে নিয়ে আগেকার শক্রর মহত্বের ওপরে নির্ভর করতে হবে। আমি যখন আমার ঘরে ফিরে আসি, তখন যেন আমার চারিদিকে অন্ধকার ঘিরে ধরেছে। মাথায় প্রচণ্ড যন্ত্রণা। যন্ত্রণা ভরা মাথাটাকে আমি বালিশ আর কম্বলের মধ্যে সজোরে চেপে ধরি।
আমি আমার মা’র কবরের পাশে যেদিন দাঁড়িয়েছিলাম, তারপরে আর কাঁদিনি। আমার ভাগ্য যত আমার প্রতি বাল্যকালের দিনগুলোয় নিষ্ঠুর নির্মম হয়ে উঠেছে, আমার মানসিক জোরও যেন ততই বেড়ে গেছে। মনে হয়েছে ইস্পাতের মত শক্ত। যুদ্ধের এ বছরগুলোতে যখন মৃত্যু এসে আমার নিকটতম বন্ধু এবং সত্যিকারের সহকর্মীকে ছিনিয়ে নিয়েছে, তখনো তার বিরুদ্ধে অভিযোগের একটা কথাও উচ্চারণ করা আমার মনে হয়েছে চরম পাপ। তারা কি জার্মানির জন্য মরেনি? এবং যুদ্ধের এ ভয়ঙ্কর শেষ কয়েকটা দিনে, যখন বিষাক্ত গ্যাস আমাকে গিলতে উদ্যত, চোখের ভেতরে বাসা বেঁধেছে, চিরদিনের মত অন্ধত্বের ভয় আমাকে ঘিরে ধরেছে। কিন্তু হৃদয়ের বাণী বেরিয়ে এসেছে, হতভাগ্য সহকর্মীরা, তোমরা কি নেকড়ের মত চিৎকার করবে যখন হাজার হাজার অন্যান্যরা তোমাদের চেয়ে খারাপ অবস্থায় রয়েছে। সুতরাং এ দুর্ভাগ্যকে আমি মেনে নিলাম, কারণ ততদিনে আমি বুঝতে পেরেছি এটাই একমাত্র খোলা পথ–এবং একটা জাতির দুর্ভাগ্যের কাছে ব্যক্তিগত কারো দুঃখের কোন মূল্যই নেই।
সুতরাং সমস্ত কিছুই নিস্ফল হয়ে দাঁড়ায়। সমস্ত আত্মোৎসর্গ এবং ক্লেশ, ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় মাসের পর মাস দিন যাপনের গ্লানি, ঘন্টার পর ঘন্টা মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে থাকারও কোন মূল্য নেই। কর্তব্যকার্যে সাড়া দিয়ে যারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে তাদের কথা চিন্তা কর–যারা হাজারে হাজারে হৃদয় দিয়ে তাদের পিতৃভূমিকে ভালবেসেছিল, কিন্তু তারা আর কখনই ফিরে আসেনি। কেউ তাদের কবরটাকেও খোলেনি যাতে সেইসব বীরদের আত্মা যা কাদা এবং রক্তের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেগুলো যেন স্বদেশে বাড়িতে ফিরে আসতে পারে, এবং যারা এ ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতায় অংশ নিয়েছে, তাদের ওপরে উল্কটরূপে প্রতিশোধ নিতে পারে। এর জন্যই কি সৈন্যরা ১৯১৪ সালের আগস্টে এবং সেপ্টেম্বরের যুদ্ধে মারা গিয়েছিল? এ কারণেই কি যুব দল সেই বছরের শুরকালে পুরনো সৈন্যদলের অনুবর্তী হয়েছিল? এর জন্যই কি সতেরো বছর বয়স্ক ছেলেরা ফ্লার্সের মাটিতে নিজেদের মিশিয়ে দিয়েছিল? এ কি হল জার্মান মেয়েদের পুরস্কার? যারা ভারী হৃদয়ে তাদের ছেলেদের উদ্দেশ্যে শুভ বিদায় জানিয়েছিল; তারা তো আর কোনদিনই ফিরে আসেনি। এসব-ই কি করা হয়েছিল একদল জঘন্য অপরাধীদের হাতে পিতৃভূমিকে তুলে দেবার জন্য?
এর জন্যই কি জার্মান সৈন্যরা উত্তাপে ক্লিষ্ট এবং অন্ধ করা বরফের ঝড়ের মধ্যে যুদ্ধ করেছিল, সহ্য করেছিল অসহ্য ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর প্রচণ্ডরকমের শৈত্য, বিদ্রি রাত আর সুদীর্ঘ পদযাত্রা? এর জন্যই কি অবিশ্রান্ত বোমাবর্ষণের নরক-দমবন্ধ করা গ্যাসের আক্রমণে কখনো টলেনি বা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালায়নি? শত্রুদের হাত থেকে পিতৃভূমির রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছে? নিশ্চিতরূপেই এসব বীরেরা সমাধির ওপরে নিচের উত্তীর্ণ লিপি পাবার দাবি রাখে :
পথিক, তুমি যখন জার্মানিতে আসবে, দেশে ফিরে গিয়ে তোমার দেশবাসীকে বল,–আমরা এখনো শুয়ে আছি। যারা পিতৃভূমির সঙ্গে একান্ত এবং নিশ্চিতরূপে তাদের কর্তব্যকর্ম করেছে।
কিন্তু এ উৎসৰ্গতাকেই আমরা কি একমাত্র বিবেচনা করব? জার্মানি কি এ অতীতের একটা দেশের মত এত কম মূল্যবান? ইতিহাসের তার প্রতি কি কোন কর্তব্য নেই? আমরা কি এখনো পর্যন্ত শুধু অতীতের গৌরবের অংশ নিয়ে সন্তুষ্ট থাকব? আমরা আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের কাছে আমাদের কাজের কি যুক্তি রাখব? এরা হল একদল জঘন্য ধরনের ভ্রষ্ট অপরাধীর দল।
আমি প্রাণপণে চেষ্টা করি (উবৃত্তি করে হলেও) এ বীভৎস ঘটনার কিছু খবরাখবর সংগ্রহ করার। যত বেশি খবরাখবর জোগাড় করি, তত বেশি আমার মাথা রাগে আর। লজ্জায় জ্বলতে থাকে। যে চোখের ব্যথায় আমি কষ্ট পেয়েছি, তার তুলনায় এ ট্র্যাজিডিকে কি আমি আখ্যা দেব?
এ দিনগুলো বহন করা ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। বিশেষ করে রাতটা কাটানোই যেন অত্যন্ত কষ্টকর; শত্রুদের দয়ার ওপরে বেঁচে থাকার ধারণাটা একমাত্র মুখ এবং অপরাধী মিথ্যাবাদীরা সঠিক বলে ভাবলেও। সেই রাতগুলোয় আমার ঘৃণা যেন আরো তীব্র হয়ে ওঠে, বিশেষ করে সে ঘৃণার চরমতম প্রকাশ ঘটে সেইসব জঘন্য অপরাধীদের প্রতি।
সে দিনগুলোতে আমার ভাগ্যও যেন আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। পরিবেশ আমাকে বাধ্য করে আমার ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তা করতে, যা আমাকে রীতিমত উদ্বিগ্ন করে তোলে। এ ভিত্তিভূমির ওপরে কোন কিছু গড়ে তোলার প্রচেষ্টাটাই কি হাস্যকর নয়? অবশেষে আমার মনে হয় এটাই হল অনিবার্য–যা ঘটেছে, যা আমি অনেক আগেই। ভয়ের সঙ্গে ভেবেছিলাম, যদিও তা মনপ্রাণ দিয়ে বিশ্বাস করিনি।
সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়ামই হল প্রথম যে কমিউনিস্ট নেতাদের দিকে বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করেছিল। তারা একহাতে রাজার হাত ধরেছে, অপর হাতে কোমরে গোঁজা ছুরি খুঁজেছে।
ইহুদীদের সঙ্গে বোঝাপড়ায় আমার কোন উপায়ই ছিল না। তাদের ব্যাপারে উদ্দেশ্যটা হল,–‘হয় অথবা নয়’।
আমার তরফে তখন আমি নিজের মনটাকে স্থির করি যে আমি রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নেব।
নভেম্বরের শেষাশেষি আমি মিউনিকে ফিরে আসি। আমার বাহিনীর কার্যালয়ে যাই, যা বর্তমানে সৈনিক সমিতির হাতে। পুরো ব্যাপারটা দেখতে গেলে শাসনব্যবস্থা যথেষ্ট অপ্রীতিকর। সুতরাং আমি আমার মনটাকে স্থির করে দেখি যে যত সত্বর সম্ভব আমি সৈন্যবাহিনী ছেড়ে যাব। আমার বিধ্বস্ত যুদ্ধ সহকর্মী আরনেস্ট স্মিডের সঙ্গে আমি ট্রাউনস্টাইলে এবং সেখানে ক্যাম্প না ওঠা পর্যন্ত অবস্থান করি। ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে আবার আমরা মিউনিকে ফিরে আসি।
সেখানকার পরিস্থিতি অপরিবর্তনশীল নয়। তা যেন বিপ্লবের দিকে দুনির্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। আইজুনারের মৃত্যু একমাত্র এ অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছিল, এবং শেষ পর্যন্ত স্বৈরতন্ত্রে সমিতিকে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করেছিল, অথবা, আরো স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে এটা ছিল ইহুদী রাষ্ট্রপুঞ্জের নেতৃত্ব, যা বিশ্বাসঘাতকতারই নামান্তর। কিন্তু এটাই ছিল (যারা এ বিপ্লবের পত্তন করেছিল। তাদের চরম লক্ষ্য।
মানসিকতার সেই সন্ধিক্ষণে আমার মনের মধ্যে অনেক রকমের পরিকল্পনা ঘোরাফেরা করছিল। সেই দিনগুলো আমি অবিরত চিন্তা করে কাটিয়েছি যে ঠিক কী করা যেতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রতিটি পরিকল্পনাই পরিত্যক্ত হয়েছে, কারণ নগ্ন সত্য হল আমি জনজীবনে একান্তভাবেই অপরিচিত। সুতরাং যে কোন বিষয়কে এগিয়ে নিয়ে। যাবার জন্য প্রয়োজনীয় প্রথম আবশ্যক জিনিসটাই আমার মধ্যে ছিল না। আমি কেন তৎকালীন কোন দলের নাম লেখাইনি তার কারণ পরে আমি ব্যাখ্যা করব।
নতুন সোভিয়েত বিপ্লব তখন মিউনিকের হাওয়ায় ছড়িয়েছে, আমার প্রথম কাজ হল সেই কেন্দ্রীয় সমিতির অনিষ্টকর চিন্তাভাবনাগুলোকে আকর্ষণ করা। ১৯১৯ সালের ২৭শে এপ্রিলের সকালে আমার গ্রেপ্তার হওয়ার কথা। কিন্তু যে তিনজনকে আমাকে গ্রেপ্তারের জন্য পাঠোনো হয়েছিল তাদের সাহস ছিল না আমার রাইফেলের মুখোমুখি হওয়ার এবং সেই কারণেই তারা উপস্থিত হয়েই সরে পড়েছিল।
মিউনিকের মুক্তির কয়েকদিন পরে আমার ওপর আদেশ আসে তদন্ত কমিশনের সামনে আমাকে উপস্থিত হতে হবে; সেই তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়েছিল দ্বিতীয় পদাতিক সৈন্যবাহিনীর বিপ্লবাত্মক কাজকর্মের বিশ্লেষণের জন্য।
এটাই হল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমার প্রথম আক্রমণ। কয়েক সপ্তাহ বাদে আবার আমার ওপরে আদেশ আসে যে সৈন্যবাহিনীর অন্যান্য সৈনিকদের সঙ্গে আমাকে একটা বক্তৃতামালায় যোগ দিতে হবে। এ বক্তৃতামালার আয়োজনের কারণ হল কিছু নির্দিষ্ট আদর্শ বারবার উচ্চারণ করে সৈনিকদের মনের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া। আমার পক্ষে এ হল একটা সুযোগ যার দ্বারা বিভিন্ন সৈনিকদের সঙ্গে আমি মিলিত হতে পারব, যাদের চিন্তাধারা একই খাতে বইছে এবং যাদের সত্যিকারের পরিস্থিতিটা সম্পর্কে আমি আলোচনা করতে পারি। আমরা সবাই প্রায় একই ধারণার বশবর্তী ছিলাম যে জার্মানিকে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে কিছুতেই বাঁচানো সম্ভব নয়; বিশেষ করে নভেম্বরের বিশ্বাসঘাতকদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায়ই নেই,–কেল্ড এবং সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা হল সেই কুখ্যাত নভেম্বরের বিশ্বাসঘাতক। যে বিপুল ক্ষতি হয়ে গেছে, তার পূরণ করা জাতির মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের পক্ষে সম্ভব নয়।
আমাদের সেই ছোট গোষ্ঠীতে আমরা সবাই একটা নতুন দল গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা চালাই। সবচেয়ে যে আদর্শগুলো এ দল গঠনের ব্যাপারে প্রাধান্য পায়, সেগুলোকে ঘিরে পরে জার্মান লেবার পার্টি স্থাপন করা হয়েছিল। এ নতুন আন্দোলনের নামকরণের ব্যাপারে আমরা যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করি যাতে এটা বিশাল জনসাধারণের হৃদয়ে আবেদন জানাতে পারে, কারণ তা না হলে আমাদের সবরকম প্রচেষ্টাই নিষ্ফল হয়ে দাঁড়াবে। এবং সেই কারণেই অনেক ভেবেচিন্তে আমরা নতুন দলের। নামকরণ করেছিলাম। সোশ্যাল রেভ্যুলুসানারী পার্টি। বিশেষ করে আমাদের নতুন দলের সামাজিক চিন্তাধারা সত্যিকারের বৈপ্লবিক ছিল।
কিন্তু এর পেছনে আরো কিছু প্রাথমিক কারণ ছিল। আমার ছোটবেলায় যেসব অর্থনৈতিক কারণগুলোয় ভুগেছি, সেগুলোর উদ্ভব মূলত সামাজিক সমস্যাগুলো থেকে, প্রত্যক্ষ এবং অপ্রত্যক্ষভাবে।
পরবর্তীকালে এ ধ্যান-ধারণাগুলোই আরো বেশি বিস্তৃতি লাভ করেছিল যখন আমি ত্রিপাক্ষিক সম্মিলিত জার্মান-নীতির কথা বিশেষভাবে অনুধাবন করি। এ নীতির জন্যই জার্মানির অর্থনৈতিক অবস্থার ভ্রান্ত মূল্যায়ন সম্ভব হয়েছিল। কারণ ভবিষ্যতে জার্মান জনসাধারণের অবস্থিতির ভুল ধারণার থেকেই এ ভ্রান্ত অর্থনীতির জন্ম হয়েছিল। এসব ধ্যান-ধারণার ভিত্তিভূমি ছিল যে পুঁজি তা হল শ্রমিকদের শ্রমের ফসল এবং একান্তভাবেই শ্রমিকদের দ্বারা উৎপন্ন এবং শ্রমিকদের মতই এটাও মানুষের কার্যক্ষমতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বা গতিরোধ করতে সক্ষম। সুতরাং জাতির স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে, এ পুঁজির রহস্য দেশের মহত্ত্ব, বিশালত্ব, শক্তির ওপরে নির্ভর করে। এক কথায় এটা জাতির ওপরেই নির্ভরশীল এবং সে কারণে দেশের স্বাধীনতাই একমাত্র এ সম্পদকে জাতির স্বার্থে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে আত্মরক্ষা এবং উন্নতির জন্য।
এ আদর্শগুলো মেনে চললে সম্পদের প্রতি দেশের মনোভাব সহজ এবং সরল হয়ে ওঠে। এর একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত যে সম্পদ পুরোপুরি দেশের অভীষ্টসাধক হবে এবং নিজস্ব কোন ক্ষমতাই থাকবে না যার দ্বারা সে জাতিকে শাসন করতে পারে। সুতরাং এর কার্যকারিতা দুটো বিষয়বস্তুর ওপরে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত। একদিকে যেমন সে জাতিকে শক্তিশালী এবং মুক্ত অর্থনীতি দেবে, অন্যদিকে শ্রমিকের দাবিগুলোকে রক্ষা করবে।
আগে আমি এত স্পষ্টভাবে সম্পদের পার্থক্য, যা নাকি স্রেফ সৃজনশীল শ্রমিকদের উৎপাদন, তা স্বীকার করে নিইনি। এবং যার অস্তিত্ব ও গতি-প্রকৃতি হল নিছক অর্থনৈতিক অনুধ্যানের ফলাফল। এখানে আমি সত্যিকারের আমার মনকে তাড়া দিয়ে সেইদিকে চালনা করি, যে শক্তির এতদিন আমার মধ্যে অভাব ছিল।
এ প্রয়োজনীয় শক্তি জোগান দেয় একজন, তার বক্তৃতা প্রসঙ্গে আমি আগেই উল্লেখ করেছি। তার নাম হল গটফিড় ফেডার।
জীবনে প্রথমবার আমি স্টক এক্সচেঞ্জও সম্পদ এবং যে সম্পদ ধারকর্জের ব্যাপারে ব্যবহার করা হয়ে থাকে — সে সম্পর্কে শুনি। ফেডারের প্রথম বক্তৃতা শুনেই আমার মস্তিষ্কে একটা ধারণা প্রবাহ খেলে যায়, যা একটা নতুন দল গঠনের পক্ষে অত্যাবশ্যক।
আমার মনে হয় ফেডারের মেধা একদিকে যেমন নির্দয়, অপরদিকে তেমনি স্পষ্টতায় ভরা, অন্ততপক্ষে যেভাবে ফেডার স্টক এক্সচেঞ্জের অন্তর্গত সম্পদের দ্বৈত চরিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরেছিল, যার থেকে এটুকু পরিষ্কার বুঝেছিলাম যে এ সম্পদ দেয় সুদের ওপরে নির্ভরশীল। বিশেষ করে গোড়ার প্রশ্নে তার বক্তব্য এত জ্ঞানযুক্ত এবং গভীর যে যারা তাকে সমালোচনা করেছিল, তারাও তাঁর বক্তব্যকে ভাল না বেসে পারেনি। কিন্তু তাদের সন্দেহ ছিল যে এটাকে কাজে লাগানো সম্ভব কিনা। যদিও অন্যান্যরা এটাকে দুর্বল বলে ভেবেছিল, কিন্তু আমার কাছে এটাই ছিল ফেডারের শিক্ষণের সবচেয়ে মূল্যবান অংশ।
যে সব তত্ত্ব তাত্ত্বিকেরা লোকের সামনে তুলে ধরে, সেগুলোকে বাস্তবে কি করে রূপায়ন করতে হবে তা বলে দেওয়া তাদের কাজ নয়। তার কাজ হল সমস্যাটার মুখোমুখি হওয়া; সুতরাং তার লক্ষ্য থাকবে সমাপ্তিতে, কোন পথ বেয়ে গিয়ে তা সমাপ্তিতে উপস্থিত হবে তাতে নয়। সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হল আদর্শটা নির্ভুল কিনা। এটাকে রূপায়িত করা সম্ভব কি অসম্ভব, সেটা আলাদা প্রশ্ন। যে মানুষের কাজ কোন নীতি বা আদর্শ বাতলানো, তাকে ব্যস্ত রেখে সেটাকে সুবিধাজনকভাবে বাস্তবে রূপায়ণ করা সম্ভব কিনা—এ দিকটাই। এর সত্যাসত্যের দিকটা তার বক্তব্য বিষয়ও নয়; যা নাকি দৈনন্দিন ব্যাপারে আলো দেখিয়ে মানুষকে তার অভীষ্ট পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। যে কোন ব্যক্তি একটা বিপ্লবের ছক আঁকে কীভাবে লক্ষ্য পৌঁছাতে হবে ভেবে। বাকিটা হল রাজনৈতিক নেতাদের কাজ। সুতরাং তাত্ত্বিকের কাজ হল চিরসত্যগুলোকে দেখিয়ে দেওয়া, আর রাজনৈতিক নেতাদের দায়িত্ব সেই সত্যগুলোকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া।
সেই তাত্ত্বিকের মহান দিক হল তার চিন্তাধারায় কতখানি সত্য উপস্থিত হতে পারে বিমূর্তরূপে। এবং অপরদিকে কর্তব্য হল সেই সত্যকে বাস্তবায়িত করা এবং তাত্ত্বিকের তত্ত্ব কতখানি সত্যের উপর দাঁড়িয়ে আছে, তা নির্ধারণ করা, এ মহত্বতাই রাজনৈতিক নেতাদের সাফল্য এবং উদ্যম এনে দেয়; যা তাকে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য করে। কিন্তু রাজনৈতিক দার্শনিকদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছান কখনই সম্ভব নয়। কারণ মানুষের চিন্তাধারা সেই সত্যটাকেই গ্রহণ করে সমাপ্তিটাকে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ দেখতে পারে। যদিও সে কোনদিনই পরিপূর্ণ সমাপ্তিতে পৌঁছতে পারবে না, কারণ মানুষের চরিত্র হল দুর্বল এবং অপরিপূর্ণতায় ভরা। সেই বিমূর্ত আদর্শগুলো যত পরিপূর্ণ হবে, তা শক্তিশালী হলেও বাস্তবে তার রূপায়ন ততখানিই অসম্ভব। অন্ততপক্ষে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই আদর্শ রূপায়ণের ভার মানুষের ওপরে থাকে। রাজনৈতিক দার্শনিকের সাফল্য বাস্তবে তার পরিকল্পনা কতদূর সফলতা লাভ করেছে তার ওপর নয়; বরং তা নির্ভর করে তাতে কতখানি সত্য উদ্ভাসিত এবং মানুষের উন্নতিকল্পে কতটুকু উদ্যম সেই আদর্শে রয়েছে। এটা যদি অন্যরকম হত, তবে ধর্মের স্রষ্টারা শ্রেষ্ঠ মানব সন্তান বলে কখনোই সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবেও বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব নয়। এমন কি ধর্ম, যেটাকে প্রেমের ধর্ম নামে অভিহিত করা হয়, তার বাস্তবে রূপায়ণ স্রষ্টার ইচ্ছার এতটুকু অংশও নয়, যা ম উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু এর পরিপূর্ণতা হল মানুষের সভ্যতার এবং নৈতিকতার উন্নতির প্রয়াসে।
রাজনৈতিক, দার্শনিক এবং বাস্তবসম্মত রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে প্রচণ্ড ফারাকের কারণ হল একই মানুষের মধ্যে এ দুই গুণের সমন্বয়ের অভাব। বিশেষ করে ছোট ধরনের সফল রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য; যাদের কার্যধারা ঘিরে থাকে সম্ভব সবকিছুকেই সফল করে তোলা; বিসমার্ক বিনীতভাবে যাদের রাজনৈতিক শিল্পী বলে আখ্যা দিয়েছে। এ ধরনের রাজনীতিজ্ঞরা যদি মহান আদর্শগুলোকে পাশ কাটাতে পারে, তবে তাদের সাফল্য সহজে আসবে। এসব কারণে এ ধরনের সাফল্য খুব একটা উপকারে আসে না এবং ক্ষণস্থায়ী হয়। এমন কি লেখকের মৃত্যুর আগেই তা বিলীনও হয়ে যায়। বিশেষভাবে বলতে গেলে রাজনৈতিক নেতাদের কাজ বর্তমান কালের জন্য নয়; কারণ তাদের তাৎক্ষণিক সাফল্যমানেই হল বিরাট সমস্যাগুলোকে পাশ কাটিয়ে দেওয়া, যে সমস্যা এবং আদর্শগুলোর মূল্যায়ণ ভবিষ্যতে হবে।
নৈতিকতার আদর্শকে ভবিষ্যতের পথে অধ্যাবসায়ের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ লাভজনক নয় এবং সর্বোপরি যে এ কাজ করে এবং এ পথ বেয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়, তাকে জনসাধারণ খুব কম সময়েই সঠিকভাবে বুঝতে পারে। কারণ তাদের কাছে বীয়ার এবং দুধ অনেক বেশি প্ররোচনামূলক, ভবিষ্যতের কোন দূরদর্শী পরিকল্পনার চেয়ে। এ পরিকল্পনার শুভ দিকটা একমাত্র ভবিষ্যতের গর্ভেই নিহিত এবং তার ফলাফল উত্তর পুরষেরাই ভোগ করতে পারে; এবং উত্তর পুরুষদের জন্যই এ পরিকল্পনার বীজ বপন করা হয়ে থাকে।
কোন নির্দিষ্ট অহঙ্কারের জন্য, যে অহঙ্কারের সঙ্গে মুখামীর রক্তের যোগাযোগ রয়েছে; সেই কারণে রাজনৈতিক নেতারা বিশেষ করে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা পরিহার করে চলে, যার বাস্তব প্রয়োগ বাস্তবিকপক্ষে কষ্টকর। তার জন্য যাতে তাকে জনসাধারণের জনপ্রিয়তা হারাতে না হয়, তাই এসব রাজনৈতিক নেতাদের সাফল্য এবং প্রয়োজন একান্তভাবেই সমকালীন। ভবিষ্যতে এদের কোন সাফল্য থাকে না। কিন্তু এ ব্যাপারটা সংকীর্ণমনাদের কোন চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটাতে পারে না, কারণ তারা তো বর্তমানের সাফল্য নিয়েই সন্তুষ্ট।
সংগঠনী শক্তিসম্পন্ন রাজনৈতিক দার্শনিকদের জায়গা একটু ভিন্ন রকমের। তাদের কাজের প্রয়োজনীয়তা ভবিষ্যতের দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝতে হবে। যার জন্য প্রায়ই তাকে শুনতে হয় সে স্বপ্নালু। রাজনৈতিক নেতাদের সাফল্য হল সম্ভাব্যতার শিল্পকে করায়ত্ত করা। রাজনৈতিক কোন আদর্শের প্রতিষ্ঠাতা, যাদের সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে তারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে, কারণ তাদের ইচ্ছা এবং অসম্ভবতার সম্ভব করার প্রবল ইচ্ছা, তারা সবসময় সমকালীন খ্যাতিকে অস্বীকার করে; কিন্তু তাদের আদর্শ যদি অমর হয় তবে উত্তর পুরুষরা তাদের স্বীকৃতি দেয়।
মানব সভ্যতার এ সুবিশাল বিস্তৃতিতে এটা কদাচিৎ হয়ে থাকে যখন রাজনৈতিক তাত্ত্বিক এবং নেতা–এ দুই গুণের সমন্বয় একজনের মধ্যে দেখা যায়। যত বেশি এ উভয় গুণের সময় দেখা যাবে, তত বেশি সেই রাজনৈতিক নেতাকে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। এ ধরনের লোকেরা তাদের শ্রম সংকীর্ণমনাদের জন্য করে না; তার লক্ষ্যে পৌঁছবার পথ শুধুমাত্র কয়েক জনেই বুঝতে পারে। তার জীবন পৃথকভাবে ভালবাসা এবং ঘৃণার সমন্বয়; সমকালীনদের প্রতিবাদ, যারা সেই মানুষটিকে বুঝতে অক্ষম, তাদের সংঘর্ষ হয় ভবিষ্যত পুরুষদের স্বীকৃতির সঙ্গে, কারণ সে তো তাদের জন্যই কাজ করে যায়।
যে মানুষ ভবিষ্যত পুরুষদের জন্য যত বেশি পরিমাণে কাজ করে, সমকালীনরা তাকে ঠিক ততখানি কম স্বীকৃতি দেয়। সে কারণে তার সগ্রামের পথটাও কঠোর হয়ে ওঠে এবং সাফল্যও ঠিক তত পরিমাণে কম পায়। শতাব্দীর পরিমাপে, যারা তাদের জীবনের শেষ প্রান্তে এ ধরনের আশীর্বাদ ধন্য হয়, তারা জীবনের সায়াহ্নকালে হয়ত বা খ্যাতির এতটুকু পূর্বাভাস পেলেও পেতে পারে। কারণ ইতিহাসের পাতায় তো তারা ম্যারাথন দৌড়বীর বলে চিহ্নিত; সমকালীন খ্যাতির মুকুট জোটে মৃত্যুপথযাত্রী এসব নায়কদের কপালে একেবারে শেষ মুহূর্তে।
তারাই হল মহান নায়ক যারা নাকি তাদের আদর্শ এবং সেই আদর্শের প্রতিষ্ঠার জন্য অবিরত সগ্রাম করে চলে, যদিও সমকাল তাদের স্বীকৃতি দেয় না। তারা হল সেই ধরনের মানুষ যাদের স্মৃতি ভবিষ্যত পুরুষদের হৃদয় আলোকিত করবে। সেই সময়। ব্যক্তিগতভাবে প্রতিটি মানুষ এসব মহান নেতা যারা সমকালীন সমাজের স্বীকৃতি পায়নি, তাদের ক্ষতিপূরণ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠে। এদের জীবন, আদর্শ এবং কর্মপদ্ধতি তখন প্রচণ্ড শ্রদ্ধা এবং ভালবাসার সঙ্গে সামনে থাকে।
এ দলে সত্যি বলতে গেলে শুধু মহান রাষ্ট্র নেতারাই পড়ে না, বড় বড় সমাজ সংস্কারকরাও এ দলভুক্ত। ফেডরিক গ্রেট ছাড়াও এমন মানুষ হল মার্টিন লুথার এবং রিচার্ড ভাগনার।
আমি যখন গটফিড ফেডারের প্রথম বক্তৃতা ‘সুদ-দাসত্বের অবলুপ্তি’ শুনি, আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে এখানেই জার্মান ভবিষ্যত বংশধরদের মনুষ্যজ্ঞানের অতীত সত্য লুকিয়ে আছে।
স্টক এক্সচেঞ্জ সম্পদকে যদি জাতির অর্থনৈতিক জীবন থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়, তবেই জার্মান ব্যবসাকে আন্তর্জাতিক অর্থনীতির প্রভাব থেকে মুক্ত করা সম্ভব। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটার প্রতিও নজর রাখতে হবে যাতে জার্মান অর্থনীতির ওপরে কোন আক্রমণ করা না হয়, কারণ তাহলে জাতির স্বাধীনতার ভিত্তিভূমিটাই বিপন্ন হয়ে পড়বে। আমি পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছিলাম জার্মানিতে কি চলেছে। ফেডারের বক্তৃতায় আমি আগামী সংগ্রামে শ্রেণীবদ্ধ কান্নাকে যেন শুনতে পাই।
ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক পরিণাম সম্পর্কে সমস্ত রকমের ধ্যান-ধারণা যা সুদ সম্পদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবে—এ চিন্তাধারাটাই ভুল। কারণ প্রথম অর্থনৈতিক নীতিগুলো এতদিন পর্যন্ত জার্মান জাতির স্বার্থে সাংঘাতিক রকমের ব্যর্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের জাতির অস্তিত্বরক্ষার স্বার্থে যে ধরনের মনোভাব গ্রহণ করা হয়েছিল এবং যা বিশেষজ্ঞরা দিয়েছিল, উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে রেলওয়ে লাইন বসাবার ব্যাপার। সেই শ্রদ্ধাস্পদ দলের সদস্যরা যে আশঙ্কা করেছিল, তা সঠিকভাবে কেউ-ই উপলব্ধী করতে পারেনি। যারা এ বাষ্পীয় অশ্বের নতুন কমপার্টমেন্টে চড়েছিল, তারা মাথা ঘোরার পীড়ায় ভোগেনি। যারা দেখেছে তারাও অসুস্থ হয়নি এবং বিজ্ঞাপনপত্রের অস্থায়ী কাঠের ফলকগুলো, যেগুলো নতুন আবিষ্কারকে লুকাবার জন্য দাড় করানো হয়েছে, শেষমেষ সেগুলোকে নামিয়ে নেওয়া হয়। একমাত্র অন্ধ যারা এবং যাদের দৃষ্টিশক্তিও অন্ধকারময়, তারাই তথাকথিত বিশেষজ্ঞ হিসেবে রয়ে গেছে। ব্যাপারটা সর্বদাই এরকম।
দ্বিতীয়ত এ ব্যাপারটাকে সর্বদা মনে রাখতে হবে যে কোন আদর্শ বিপদের কারণ হতে পারে যদি এটাকে সমাপ্তি বলে ধরে নেওয়া হয়; যখন সত্যিকারের এটা শেষ নয়। আমার এবং সমস্ত সত্যিকারের জাতীয়তাবাদীদের কাছে মতবাদ বলতে মাত্র একটাই,–জনসাধারণ এবং পিতৃভূমি।
এখন একান্ত প্রয়োজন হল আমাদের অস্তিত্বরক্ষার জন্য সংগ্রাম এবং আমাদের জাতের লোক বৃদ্ধি; এদের সন্তানদের সত্তা বজায় রাখা এবং আমাদের জাতিকে অবিমিশ্র করে রাখা। পিতৃভূমির স্বাধীনতা যাতে বজায় থাকে তার দিকে নজর দেওয়া, অর্থাৎ আমাদের লোকদের ওপর স্রষ্টা যে কর্তব্য চাপিয়ে দিয়েছে তারা যাতে তার সমাধান করতে পারে।
সমস্ত রকম আদর্শ এবং আদর্শবাদীতা, সমস্ত রকমের নীতি এবং জ্ঞানের লক্ষ্য হল এ সমাপ্তিতে পৌঁছানো। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই সবকিছু পরীক্ষা করা উচিত এবং তারপর সেগুলোকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ বা বাতিল করা সংগত। এভাবে একটা তত্ত্ব শুধু মৃত ধর্ম মতে যাতে পরিণত না হয়; কারণ সেগুলোকে তো জীবনের প্রাত্যহিক কাজকর্মে কাজে লাগাতে হবে।
গটফেড ফেডারের মতামত শুনে আমার মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায় বিষয়টার গভীরে যাওয়ার এবং আমাদের অনুপ্রাণিত করে এমনভাবে প্রশ্নটাকে দেখায় যা আমি আগে ভাবিনি বা সেই ধ্যানধারণার সঙ্গে আমার আগে পরিচয় ছিল না।
আমি আবার পড়তে শুরু করি এবং এভাবে প্রথম আমি সঠিকভাবে বুঝতে পারি সে ইহুদী কার্লমার্কসের উদ্দেশ্য এবং জীবন। তার লেখা ‘দাস ক্যাপিটেল’ বইটার উদ্দেশ্য আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। সে আলোতে আমি এখন পরিষ্কার বুঝতে পারি জাতীয় অর্থনীতির বিরুদ্ধে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের সংগ্রামটা। এ হল আন্তর্জাতিক এবং স্টক এক্সচেঞ্জের সম্পদের নেতৃত্ব পাওয়ার যোগ্য।
আমার জীবনের অন্যান্য দিকে এ বক্তৃতার প্রভাব সুস্পষ্ট ভাবেই পড়েছিল।
একদিন বিতর্কে অংশগ্রহণ করার জন্য আমি আমার নাম লেখালাম। সেই বিতর্কে অংশগ্রহণকারী আরেকজন ভেবেছিল যে সে ইহুদীদের জন্য তৈরি বর্শাটা ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেবে; সেই কারণে সে তাদের পক্ষ অবলম্বন করে দীর্ঘ এক আলোচনায় প্রবেশ করে; এটাকে বিরোধিতা করার জন্যই আমি উঠে দাঁড়াই। সংখ্যাগরিষ্ঠ উপস্থিত সভ্যরা আমার দৃষ্টিভঙ্গিকেই সমর্থন জানায়। এর ফলে মিউনিকে অবস্থিত সৈন্যবাহিনীতে আমি ইনস্ট্রাকসন অফিসারের পদ পাই, মাত্র কদিন পরেই।
সে সময়ের সৈন্যদলের মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব ছিল। এরা তখন সৈনিক সমিতির নেতৃত্বের পরের অবস্থার ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। একমাত্র সতর্কভাবে এবং ধীরে ধীরে নতুন একটা সামরিক শৃঙ্খলাবোধ এবং বাধ্যতা, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বাধ্যতার জায়গায় চাপিয়ে দিতে পারলে, যাকে কূট আইজনারের বিশৃঙ্খল বাহিনীকে যে আদর্শ সামরিক শৃঙ্খলাবোধ ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল, তা সম্ভব। সৈনিকদের মধ্যে জাতীয়তাবাদী এবং দেশপ্রেমিকের শিক্ষা ও অনুভূতি জাগিয়ে তোলার প্রয়োজন। এ দু’টোই হল আমার ভবিষ্যত কর্মপন্থা।
আমি আমার কাজ শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রমের সঙ্গে হাতে তুলে নিলাম। এবারে আমার বিরাট শ্রোতাদের কাছে বক্তৃতা দেবার সুযোগ আসে। আমি নিশ্চিত হই, যেটা আগে মাত্র অনুভূতির স্তরে ছিল, সেই বক্তৃতা দেওয়ার একটা সহজাত ক্ষমতা আমার ভেতরে আছে। আমার গলা স্বর প্রক্ষেপণ এতই চমৎকার যে সবাই আমার বক্তৃতা স্পষ্ট শুনতে পারে। অন্ততপক্ষে ছোট্ট ঘরে সমবেত সৈনিকদের তো কোন অসুবিধাই হবার কথা নয়।
এ কাজের চেয়ে পৃথিবীতে আর কোন কাজই আমাকে এতখানি সুখী করতে পারত; সামরিক বাহিনী ছেড়ে দেওয়ার আগে আমার কর্তব্য এমন একটা প্রতিষ্ঠানের প্রতি করতে পেরে আমি আনন্দিত, যে প্রতিষ্ঠানটা আমার হৃদয়ের সবচেয়ে কাছাকাছি,–হ্যাঁ, সেই সামরিক বাহিনী।
আমি বলতে পেরে সুখী যে আমার দেওয়া বক্তৃতাগুলো সফল হয়েছিল। আমার বক্তৃতা দেওয়ার সময়ে শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে আমার দেশবাসীকে তাদের লোকদের এবং পিতৃভূমির কাছাকাছি নিয়ে আসতে পেরেছি।
আমি সৈন্যবাহিনীকে জাতীয়করণ করি; যার দ্বারা সামরিক বাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়।
এখানেও আমি আবার বেশ কিছু সহকর্মীর সাক্ষাৎ পাই, যাদের চিন্তাধারার সঙ্গে আমার চিন্তাধারা অভিন্ন। এবং সে কারণে তারা আমার দলে এসে ভেড়ে এবং আমরা নতুন একটা আন্দোলন গড়ে তুলি।
০৮. জার্মান শ্রমিক দল
একদিন হঠাৎ আমার ওপরে আদেশ আসে একটা সংঘ যাকে আপাতদৃষ্টিতে রাজনৈতিক দল বলে মনে হয়, তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার। এরা নিজেদের বলত ‘দ্য জার্মান লেবার পার্টি এবং শীঘ্রই তারা একটা মিটিং ডাকছে যাতে গফি বক্তৃতা দেবে। আমার ওপরে আদেশ হল সেই মিটিংয়ে উপস্থিত থাকতে এবং পরিস্থিতির বিশদ বিবরণ জানতে।
যে রহস্যময়তার চোখে সৈন্যবাহিনীর কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক দলগুলোকে দেখত তা ভালভাবেই জানতাম। বিপ্লব সৈন্যবাহিনীকে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছে। কিন্তু যারা এ সুযোগ নিয়েছে,অভিজ্ঞতা বলতে তাদের নেহাত-ই খুব কম ছিল। কিন্তু যতদিন না পর্যন্ত কেন্দ্র এবং সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি অনিচ্ছাভরে জোর করে বুঝতে পেরেছে যে, সৈনিকদের সহানুভূতি বিপ্লবের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দিকে গেছে এবং জাতির ভোট দেওয়ার অধিকার এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ বন্ধ করেনি।
সত্যি বলতে কি কেন্দ্র এবং মার্কসবাদের এ নীতি রীতিমত শিক্ষাপ্রদ; কারণ তারা যদি ভোটাধিকার খর্ব না করত–যা বিপ্লবের পথে সৈন্যবাহিনীর রাজনৈতিক দাবি বলে স্বীকৃত; যে সরকার ১৯৩১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কয়েক বছরে তাকে উপড়ে ফেলে দিত তাতে জাতির অসম্মান ও দুর্দশা আরো বেশি দীর্ঘায়িত হত। সেই সময় সৈন্য এবং জাতির মধ্যে সম্পর্কটা ছিল রক্তশোষক পিশাচের মত, যার কাজ হল অন্তমৈত্রী বজায় রাখা। কিন্তু এটাও সত্যি যে তথাকথিত জাতীয় দল অত্যুৎসাহের সঙ্গে অপরাধী মনোবৃত্তির মনোভাব সম্পন্ন লোকদের নির্বাচিত করেছিল, যারা ১৯১৮ সালের বিপ্লবকে সমর্থন জানিয়ে সৈন্যবাহিনীকে জাতির জাগরণের ক্ষেত্রে একটা অকেজো যন্ত্রে পরিণত করেছে। এবং এ সত্যটাকে একদল সহজে প্রতারিত মানুষ মেনেও নেয়।
বুর্জয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মনোভাব জমে গিয়ে এমন পাথরের মত শক্ত হয়ে গিয়েছিল যে, তারা মনে মনে সত্যিই বিশ্বাস করতে শুরু করে যে সৈন্যবাহিনী আবার নিজেদের জায়গাতেই ফিরে আসবে, যা নাকি জার্মান শৌর্যবীর্যের দুর্গ প্রাচীর বলে পরিগণিত।
এ সময় কেন্দ্রীয় দল এবং মার্কসবাদীরা জাতীয়তাবাদীর বিষাক্ত দাঁতগুলো তুলতে ব্যস্ত। তাছাড়া সৈন্যবাহিনী একটা বৃহত্তর পুলিশ দলে পরিণত হবে তাদের সামরিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে; এবং তাহলে তো বহিঃশত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করাই তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। পরের ঘটনাবলী দ্বারা এর সত্যাসত্য যথেষ্ট পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হয়।
আমাদের জাতীয় রাজনৈতিক নেতারা কি বিশ্বাস করেছিল যে, আমাদের সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি জাতীয়তাবাদীতার পথে নয়, অন্যদিকে? সম্ভব এ বিশ্বাসই তাদের। মধ্যে ছিল। কারণ যুদ্ধের সময়ে তো তারা প্রকৃত সৈন্য ছিল না, ছিল একদল বাচাল। অন্য কথায় বলা যেতে পারে, তারা ছিল সংসদীয় সদস্য এবং যে কারণে সাধারণ জনসাধারণের হৃদয়-সম্পর্কে এতটুকু খোঁজখবর রাখত না। যারা অতীতের স্মৃতি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকত এবং সর্বদা স্মরণ করত যে একদা তারা সর্বশ্রেষ্ঠ সৈনিক বলে পরিগণিত ছিল।
আমি স্থির করি যে এ মিটিংয়ে যোগদান করতেই হবে, যা নাকি আমার কাছে একেবারেই অজানা। আমি যখন ভূতপূর্ব স্টারনেকার পানশালার অতিথি ঘরে হাজির হই, যা এখন আমাদের কাছে ঐতিহাসিক একটা বস্তু বলে পরিগণিত–দেখি কুড়ি পঁচিশজন লোক উপস্থিত, বেশিরভাগই সমাজের নিচু স্তর থেকে আসা।
ফেডারের বক্তৃতার ধ্যান-ধারণার সঙ্গে আমার আগেই পরিচিতি ছিল; কারণ আমি যে তার বক্তৃতা আগেই শুনেছি তা তো বলেছি। সুতরাং সঙ্টার পর্যবেক্ষণের কাজে আমি মনোনিবেশ করি।
এদের সম্পর্কে আমার ধারণা খারাপ হয় না, আবার ভালও হয়নি। আমার মনে হয় সেই সময় ভুইফোড় অনেক সঙ্ সমিতির মধ্যে এটাও একটা। সেই দিনগুলোতে প্রত্যেকেই এক একটা নতুন দল গড়তে চাইত। অর্থাৎ যে সমকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে ভীতশ্রদ্ধা বা তখনকার দিনের দলগুলো সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং এ সঙ্গুলো যেমন হঠাৎ রাতারাতি গজিয়ে উঠত, তেমনি নিমেষে মিলিয়েও যেত; আর কোন প্রতিক্রিয়া কোথাও অনুভব করত না। সত্যি বলতে কি এসব স সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না যে অসংখ্য লোককে একত্রিত করে সঙ্ঘ বা সমিতি প্রতিষ্ঠার অর্থ কি বা আন্দোলন বলতে ব্যাপারটা কি বোঝায়। সুতরাং এসব ভূঁইফোড়দের সঙ্গুলো রাতারাতি অদৃশ্য হত। তাদের পরিস্থিতির প্রয়োজন সম্পর্কে কোন ধ্যান-ধারণাই ছিল না।
ঘণ্টা দুয়েক ওদের কার্যবিবরণী শোনার পর জার্মান লেবার পার্টি সম্পর্কে আমার ধারণা খুব একটা বদলায় না। ফেডার শেষমেষ তার বক্তৃতা সাঙ্গ করলে পরে আমি সুখী হই। আমার ততক্ষণে যথেষ্ট পর্যবেক্ষণ হয়ে গিয়েছিল এবং যখন আমি প্রায় উঠতে উদ্যত, তখনই ঘোষণা করা হয়–যে কেউ এর ওপর খোলা বিতর্কে অংশগ্রহণ করতে পারে। এটা শুনে আমি সেখানে থাকাটাই স্থির করি। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আমার ধারণা হয়, বিতর্কটা প্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলো ছেড়ে দিয়ে অপ্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ নিয়েই যেন বেশি মেতে উঠেছে, তখনই হঠাৎ ‘অধ্যাপক’ কথা বলতে শুরু করে। তার বক্তৃতার মুখবন্ধই হয়, ফেডার যেসব বিষয়ে বলেছিল তাতে সন্দেহ প্রকাশ করে। এবং ফেডার তার প্রত্যুত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপকটি ‘তত্ত্বের গভীরে’ বলে আলোচনার মোড় ঘোরায়। কিন্তু এর আগে তার বক্তব্য ছিল যে ব্যাভরিয়া প্রুশিয়া ছেড়ে বেরিয়ে আসার জন্য এ নতুন দলটির প্রধান পরিকল্পনা নেওয়া উচিত। এবং একান্ত আত্মবিশ্বাস নিয়ে এ মানুষটি বলে যে জার্মানি-অস্ট্রিয়ার উচিত ব্যাভেরিয়ার সঙ্গে সংযুক্তি, তবেই শান্তি আরো ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সে আরো একটা অবিবেচকের মত বক্তব্য রাখে, এ সময়ে আমি কিছু বলার জন্য সভার অনুমতি প্রার্থনা করি এবং সেই শিক্ষিত লোকটিকে। আমার চিন্তাধারা ব্যাখ্যা করি। ফলে সেই সম্মানিত ব্যক্তিটি যে শেষ বক্তৃতা করেছিল চাবুক খাওয়া খেকি কুকুরের মত, তার জায়গা ছেড়ে দিয়ে নিপে পলায়ন করে। আমি যখন আমার বক্তব্য রাখছিলাম, শ্রোতারা একমুখ বিস্ময় নিয়ে আমার বক্তব্য শুনছিল। ঠিক যখন আমি সভাকে শুভরাত জানিয়ে বিদায় নিতে উদ্যত, একজন লোক সত্বর আমার কাছে এসে নিজের পরিচয় দেয়। আমি তার নামটা সঠিক ধরতে পারিনি; কিন্তু সে আমার হাতে একটা ছোট্ট বই ধরিয়ে দেয়, যা নাকি হল একটা রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন, এবং সে আমাকে সবিনয়ে অনুরোধ করে সেটা পড়ার জন্য।
সত্যি বলতে কি, ব্যাপারটাতে আমি খুশি-ই হই; কারণ এ রাস্তায় সংঘের উদ্দেশ্য বুঝতে অনেক বেশি সাহায্য হবে; যার জন্য ক্লান্তিকর মিটিংগুলোতে উপস্থিত হবার প্রয়োজন নেই। উপরন্তু লোকটাকে সাধারণ মজুরের মত দেখতে বলে আমার মনের ওপর ভাল একটা ছাপ রেখে যায়। এরপর আমি সভাগৃহ ছেড়ে যাই।
সেই সময়ে আমি দ্বিতীয় পদাতিক বাহিনীর একটা ব্যারাকে থাকতাম। আমার ছোট্ট ঘরটাতে তখনো বিপ্লবের ছাপ আমাকে বিরক্ত করে তুলত। দিনের বেলাতে তো বেশিরভাগ সময় বাইরে বাইরে কাটাতাম, একচল্লিশ নম্বরের হাল্কা পদাতিক বাহিনীর কোয়ার্টারে অথবা অন্য কোথাও বক্তৃতা শোনার ধান্ধায়, যা নাকি সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হত। বসবাস উপলক্ষে শুধুমাত্র রাতটাই আমি আমার কোয়ার্টারে কাটাতাম। যেহেতু ভোর পাঁচটাতে আমার ঘুম ভেঙে যেত সেইজন্য বাকি সময়টা আমি নেংটি ইঁদুরগুলো যে ঘরময় ছুটাছুটি করত, তাদের দেখেই কাটাতাম। একখণ্ড রুটির শক্ত টুকরো বা গুঁড়ো মেঝেতে ছড়িয়ে দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম, ছোট্ট প্রাণীগুলো সেই খাবারের চারপাশে খেলা করছে, এবং ভীষণ আনন্দে তাদের কাছে উপাদেয় খাবার খাচ্ছে। আবার ঘুম না আসাতে হঠাৎ আমার সেই ছোট্ট রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনের কথা মনে পড়ে যায়, যেটা নাকি একজন শ্রমিক মিটিংয়ে দিয়েছিল। ছোট্ট বইটার লেখকও সেই বইটাতে বর্ণনা দিয়েছে কেমন করে সে গলার থেকে মার্কসবাদের শৃখলটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর শব্দ দ্বারা সাজানো ট্রেড ইউনিয়নকেও। এবং তারপরেই সে জাতীয়তাবাদী আদর্শে ফিরে এসেছে। সেই কারণেই বইটার নাম রেখেছে ‘আমার রাজনৈতিক জাগরণ’; বিজ্ঞাপনটা পড়ার প্রথম মুহূর্ত থেকেই আমার মনকে টানে এবং শেষ পর্যন্ত সেই উসাই সমভাবে বজায় থাকে। যে পদ্ধতির বর্ণনা এখানে রয়েছে, দশবছর আগের আমার অভিজ্ঞতাও একই রকমের। অবচেতন মনে আমার নিজের অভিজ্ঞতা যেন নড়ে চড়ে ওঠে। সেইদিন আমি যা পড়েছি তা বারবার আমার মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমি মনস্থির করি যে ব্যাপারটায় আর মনোযোগ দেব না। প্রায় সপ্তাহখানেক পরে আমি একটা পোস্টকার্ড পাই, এবং বিস্ময়ে পড়ে দেখি যে আমাকে জার্মান লেবার পার্টির সদস্যভুক্ত করে নেওয়া হয়েছে। আমাকে অনুরোধ করা হয়েছিল যোগাযোগ করতে এবং পরের বুধবারের পার্টিকমিটির মিটিংয়ে যোগদানের জন্য।
এভাবে সভ্য করার ব্যাপারটা আমাকে কিছুটা হতবুদ্ধি করে দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই; এবং আমি ভেবেই পাইনি যে ব্যাপারটাতে রাগ করব নাকি হাসব। কেননা তখন পর্যন্ত বর্তমান কোন পার্টির সভ্য হওয়ার ইচ্ছে আমার ছিল না। বরং নিজের একটা পার্টি গড়ে তোলার দিকেই আমার ঝোঁক ছিল। এ ধরনের নিমন্ত্রণ আমি কখনো কল্পনাতেও আনতে পারিনি।
আমি প্রায় একটা উত্তর লিখে ফেলেছিলাম; কিন্তু কৌতুকের দরুণ উত্তর না দিয়ে সেই মিটিংয়ে নির্দিষ্ট দিনে যোগ দেওয়াটাই মনস্থির করি। যাতে ব্যক্তিগতভাবে এদের কাছে আমার আদর্শগুলোকে তুলে ধরতে পারি।
অবশেষে বুধবার এল। যে শুঁড়িখানায় এ মিটিংয়ের বন্দোবস্ত হয়েছিল, সেটা হল হেরেনস্ত্রানের ‘আল্টে রোজেনবাড’, যাতে হঠাৎ ছাড়া খদ্দের সচরাচর ঢুকত না। ১৯১৯ সালে এটা কোন আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়। যখন বিলগুলো বেশ উঁচু অঙ্কের আসত যদিও ভাণ দেখানো হত এমন কিছু নয়; কিন্তু খদ্দেরদের পক্ষে তা লোভনীয় নয়। যাহোক, এ রেস্তরাঁর নাম আমি আগে কখনো শুনিনি।
প্রায় অন্ধকার খদ্দেরদের বসার ঘর দিয়ে ঢুকে, সেখানে অবশ্য একটা খদ্দেরও বসে নেই, পাশের ঘরে যাওয়ার দরজা হাতড়াই; এবং দরজা খুলে দেখি সেখানেই সভা বসেছে। গ্যাসের মলিন আলোর নিচে জনা চারেক লোক একটা টেবিল ঘিরে বসে। তার মধ্যে একজন সেই বিজ্ঞাপনপত্রের লেখক। সে আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে সাদরে জার্মান পাটির একজন নতুন সদস্য হিসেবে বরণ করে।
সত্যি বলতে কি যখন শুনলাম দলের প্রেসিডেন্ট তখনো এসে পৌঁছায়নি, একটু নিরুদ্যম হয়ে পড়ি। যাহোক মনে মনে তৎক্ষণাৎ স্থির করে ফেলি যে সে এসে উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত নিজেকে প্রকাশ করব না। শেষে একসময় প্রেসিডেন্টের আবির্ভাব হয়। স্টারনেকার শুঁড়িখানার মিটিংয়ে, যেখানে ফেডার বক্তৃতা দিয়েছিল এবং যে চেয়ারম্যানের পদ অধিকার করেছিল, এ সেই ব্যক্তি।
আমার কৌতূহল জেগে ওঠে এবং সাগ্রহে অপেক্ষা করি কি হতে যাচ্ছে তা দেখার জন্য। আমি তখন সেই নামগুলো এবং ভদ্রলোকদের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ পাই, এ দলে যারা সর্বেসর্বা। দেশব্যাপি দলের প্রেসিডেন্ট হল মিস্টার হেরার আর মিউনিক জেলা পার্টির প্রেসিডেন্ট হল এনটুন ড্রেসেলার।
আগের দিনের সভার কার্য বিবরণী পড়া হয় এবং ভোটে তা যথাসময়ে গৃহীতও হয়। এরপরে আসে কোষাধ্যক্ষের রিপোর্ট। সমিতির সবশুদ্ধ মোট তহবিল হল সাত মার্ক পঞ্চাশ ফেনিগ। (তখনকার ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় তিরিশ টাকার মত।) সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য কোষাধ্যক্ষ তার মতামত ব্যক্ত করে যে সমিতির সভ্যদের ওপর তার পূর্ণ আস্থা বিদ্যমান। এটাও সভার কার্য বিবরণীর মধ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়। এরপরে আসে চেয়ারম্যান যেসব পত্রাদির উত্তর ইতিমধ্যে দিয়েছে, সেইগুলো পড়া হয়। প্রথমে কীল থেকে আসা একটা চিঠি, এর পরেরটা ডুসেলডর্ফের, শেষেরটা এসেছে শহর বার্লিন থেকে। তিনটে চিঠির উত্তরই যথাযথ দেওয়া হয়েছে বলে সমিতির অনুমোদন লাভ করে; এরপরে পড়া হয় সদ্য আসা চিঠিগুলো। বার্লিন, কীল এবং ডুসেন্ডফ থেকে আসা। ভাবভঙ্গিতে বোঝা যায় এ চিঠিগুলো আসাতে সবাই খুব খুশি। কারণ এ চিঠিগুলো আসাতে প্রমাণিত হয় যে জার্মান লেবার পার্টি সাধারণের জনপ্রিয়তা পাচ্ছে। কিন্তু তারপর? তারপরে আসে সদ্য আসা চিঠিগুলোর কি উত্তর দেওয়া হবে, তার ওপর লম্বা বিতর্ক।
ব্যাপারটা দুঃখজনক। দলবেঁধে আড্ডা মারার এটা হল নিকৃষ্টতম একটা উদাহরণ। আর আমাকে কিনা এ ধরনের একটা সমিতির সভ্য হতে হবে?
নতুন সভ্য সংখ্যার ব্যাপারটাও আলোচিত হয়–এককথায় বলা যায় সমস্ত আলোচনাটার উদ্দেশ্যই হল আমাকে কিভাবে ফাঁদে ফেলা যায়।
আমি এবার প্রশ্ন করতে শুরু করি। কিন্তু অচিরেই বুঝতে পারি কয়েকটা ভাল আদর্শ ছাড়া এদের কোন পরিকল্পনা নেই। বিজ্ঞাপনপত্র নেই, ছাপা বলতে কিছুই নেই। মেম্বারশিপের কার্ড, এমন কি দলের রবার স্ট্যাম্পও নেই। আছে শুধু বিশ্বাস আর কিছু ভাল কাজ করার ইচ্ছা।
আমার আর হাসি আসে না। এসব কিসের জন্য করা হচ্ছে। এসব হচ্ছে হতবুদ্ধিতা আর চরম নৈরাশ্যের চিহ্ন যা প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোই গায়ে সেঁটে বসে আছে। তাদের কোন পরিকল্পিত দৃষ্টিভঙ্গি নেই। যে অনুভূতির দ্বারা প্রবৃত্ত হয়ে এ কয়েকটা যুবক ছেলে এ কাজে নেমেছে, ওপর থেকে তা হাস্যকর দেখালেও অন্তরের প্রেরণাই তাদের বলেছে,–স্বতঃপ্রণোদিত হলেও সজ্ঞানে–সমস্ত দলীয় শক্তি যেভাবে বর্তমানে নিয়োজিত, তা ঠিক এমন ধরনের শক্তি অবশ্যই নয় যা জার্মান জাতিকে পুনরুদ্ধার করতে পারে বা অতীতে জার্মানরা জাতির যে ক্ষতিসাধন করেছে, জাতির অক্ষমতা দখল করে তা সারানো সম্ভব নয়। আমি তাড়াতাড়ি আদর্শগুলোর ওপরে চোখ বুলিয়ে নেই, যে আদর্শগুলোকে ভিত্তি করে পার্টি গড়া হয়েছে। একটা টাইপ করা কাগজে লিস্টটা ছাপানো। এখানেও আবার আমি বুঝতে পারি যে এরা আকুল হয়ে কিছু খুঁজে চলেছে, কিন্তু কার সঙ্গে যে সংগ্রাম করে চলেছে তার কোন চিহ্ন এতে নেই। যে অনুভূতির দ্বারা এরা চালিত হচ্ছে, আমি তা উপলব্ধি করতে পারি। এটা যে আন্দোলনের পথের সন্ধান করে চলেছে, তাকে দলের ওপরে ঠাঁই দিতে হবে এবং শুধু শব্দের মালা গাঁথলেই হবে না।
সন্ধ্যেবেলায় যখন আমি আমার ব্যারাকে ফিরে আসি, ততক্ষণে সমিতিটা সম্পর্কে আমি একটা নির্দিষ্ট ধারণা করে ফেলেছি এবং জীবনে একটা কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হই। এ দলে যোগদান করবো, নাকি একে অস্বীকার করব?
বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে আমার প্রতিটি চিন্তাধারা এ দলে সভ্য হিসেবে যোগদান করতে বাধা দিতে থাকে। কিন্তু আমার অনুভূতিগুলো আমাকে জ্বালাতন করতে শুরু করে। যত বেশি আমি নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করি যে এ সঘটায় যোগদান করা কতখানি নিরর্থক, তত বেশি আমার অনুভূতি সেদিকেই ঝুঁকে পড়ে। এ দিনগুলো আমার অস্থিরভাবেই কাটে।
আমি এর স্বপক্ষে এবং বিপক্ষের যুক্তিগুলো নিজের মনের মধ্যে আলোচনা করতে শুরু করি। দীর্ঘদিন ধরেই স্থির করেছি যে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করব। এবং এটা আমার কাছে জলের মত পরিষ্কার যে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নিতে হলে আমি কোন একটা আন্দোলনের মাধ্যমেই তা করব। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত মনের ভেতরে সত্যিকারের কোন তাড়না এ সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্য অনুভব করিনি। আমি সেই দলের লোক নই, যারা নতুন কিছু লোভে আজ একটা কিছু করে, আবার কালই তার থেকে সরে দাঁড়ায়। কারণ তার জন্য আমার সব স্বপ্নগুলো বাস্তবায়িত হওয়া প্রয়োজন, অথবা একেবারেই শুরু না করা উচিত। কেননা আমি জানতাম যদি একবার অভিমত দেই, তবে সেই মতামত আমাকে সারাজীবনের জন্য বেঁধে ফেলবে, যার থেকে ফেরার আর কোন পথ নেই। আমার পক্ষে আলস্য করে সময় নষ্ট করা সম্ভব নয়, যা কিছু করব দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এবং গভীর আগ্রহের সঙ্গেই তা সম্পাদনা করব। আমার মনের মধ্যে এমনিতেই যারা সবকিছু করতে এগিয়ে এসে শেষ পর্যন্ত সমাপ্তিতে পৌঁছায় না, তাদের প্রতি গভীর অনীহা বর্তমান। এ তথাকথিত সব বিষয়ের পণ্ডিতদের আমি ঘৃণা করি এবং এটাও আমার ধারণা যে এদের পক্ষে কোন রকম কাজ না করে চুপচাপ থাকাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।
ভাগ্য আমার আগামী রাস্তার প্রতি অঙ্গলি নির্দেশ করে। আমি কখনই বৃহৎ কোন দলে নাম লেখাব না; কারণটা পরে বিস্তারিত বলছি, এ হাস্যকর ছোট্ট সমিতিটা, সঙ্গে মুষ্টিমেয় সদস্য নিয়ে আমার ধারণায় প্রস্তরৎ অস্থি পিঞ্জরে পরিণত হবে না এবং এখানে। সম্ভবত ব্যক্তিগতভাবে কোন কাজ দেখানোর বা করার সুযোগ পাওয়া যাবে। যেহেতু আন্দোলনটা এখনো ছোট্ট গণ্ডীর ভেতরে আবদ্ধ, সুতরাং সেখানে এখনো সক্রিয় কোন কাজ করা সম্ভব। প্রয়োজন শুধু এর অবয়ব গঠনের। আন্দোলনটার চরিত্র গঠন করা যাবে। কি লক্ষ্য এবং কোন রাস্তায় গিয়ে সেই সমাপ্তিতে নিয়ে যাওয়া যায়,–এ জিনিসগুলো বড় কোন পার্টিতে গিয়ে স্থির করা সম্ভব নয়।
যত আমি চিন্তা করি তত যেন আমার মনে হতে থাকে যে জাতির পুনরুত্থানের জন্য এটাকে যন্ত্র হিসেবে চমৎকার ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু কোন সংসদীয় রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে এ কাজ করা কখনই সম্ভব নয়। তারা কতগুলো সেকেলে ধ্যান-ধারণাকে আঁকড়ে ধরে বসে আছে। অথবা নতুন কোন শাসন প্রণালীকে সমর্থনের জন্য উদগ্রীব। এখানে বর্তমানে যা প্রয়োজন তাহল সর্বজন স্বীকৃত একটা মতবাদ, ভোটের জন্য। কান্নাভরা আবেদন নয়।
কিন্তু চিন্তা করা এক জিনিস আর সেই চিন্তাধারাকে রূপ দেওয়া আরেক জিনিস; পরের অংশটা সত্যই কষ্টকর। কি কি গুণ থাকলে এ ধরনের চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব?
সত্যি বলতে কি আমি গরীব, এবং রুজি রোজগার বলতেও আমার কিছু ছিল না; তাই আমার ধারণায় বাস্তব দুঃখ-কষ্টগুলোকে আমি সহজেই বহন করতে পারব। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা হল যে আমি একেবারেই অপরিচিত। আমি হলাম সেই লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে একজন, ভাগ্যের জোরেই যারা টিকে আছে, বা টিকে থাকার অধিকার হারিয়েছে। পরের দরজার প্রতিবেশীরও যার অস্তিত্ব অজানা। আরেকটা ব্যাপারে অসুবিধে দেখা দেয় যে আমি নিয়মিত স্কুলে পড়াশুনা করিনি।
তথাকথিত বুদ্ধিমানেরা এখন পর্যন্ত অশেষ অহঙ্কারের সঙ্গে তাদের দিকে তাকায়, যাদের স্কুলের প্রশংসাপত্র নেই এবং যথেচ্ছ জ্ঞান তারা তাকে দিয়ে চলে। একটা মানুষ কি করতে পারে, সেই প্রশ্ন তারা কখনো জিজ্ঞাসা করে না; বরং তাদের যত জিজ্ঞাসা তাহল সে কতদূর পড়াশুনা করেছে, সেই প্রশ্নকে ঘিরে। তথাকথিত শিক্ষিত লোকেরা স্কুল কলেজের প্রশংসাপত্র সঁটা ক্ষীণ দুর্বল মানুষকে সত্যিকারের সক্ষম ব্যক্তির থেকে অনেক উঁচুতে স্থান দেয়, কারণ সে ব্যক্তির গায়ে চিত্রবিচিত্র করা প্রশংসাপত্র সাঁটা। সুতরাং আমার কাছে সহজেই অনুমেয় এ শিক্ষিত লোকেরা আমাকে কি চোখে দেখবে এবং এখানেও আমি ভুল করেছিলাম। কারণ আমার ধারণায় বেশির ভাগ লোকই ভাল; কিন্তু বাস্তবের শীতল আলোতে আমার এ ধারণা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। কারণ তাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন ব্যক্তিক্রম এবং বোধগম্য। আমি কিছুদিনের মধ্যে এদের ভেতরকার পার্থক্যটা বুঝতে শিখি, যারা সর্বদা স্কুলের দেওয়ালের সঙ্গে সঁটা এবং যাদের ভবিষ্যতে বাস্তব জ্ঞানের সম্ভাবনা আছে।
অনেক চিন্তা-ভাবনার পরে আমি এ মতামত নেওয়ার জন্য মনস্থির করি।
এটা ছিল আমার পক্ষে চূড়ান্ত রকমের একটা মতামত নেওয়ার পালা। কারণ এদিক থেকে ভবিষ্যতে আর মুখ ফেরানো সম্ভব নয়।
এ ভেবে আমি জার্মান লেবার পার্টির সদস্য হবার তালিকাভুক্তির জন্য স্বীকৃতি জানাই এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সাময়িক সদস্যভুক্তির সার্টিফিকেট পেয়ে যাই। আমার ক্রমসংখ্যা নির্দিষ্ট হয় সাত।
০৯. দ্বিতীয় রাইখের বিপর্যয়ের কারণ
পতনের গভীরতার পরিমাপ হল তার আসল জায়গার উচ্চতার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার বিয়োগাঙ্ক। একটা জাতির এবং রাষ্ট্রের পতনের পরিমাণের ক্ষেত্রেও এ কথাটা সত্য। স্থানের উচ্চতার পরিমাপ, অথবা সোজাসুজি বলতে গেলে বলতে হয় অবরোহণের পূর্বে তার সবচেয়ে উচ্চস্থানে অবস্থানের অঙ্কটা।
যা সবচেয়ে উঁচু জায়গায় একদা আরোহণ করেছিল, সেখান থেকেই পতন বা বিপর্যয়ই প্রত্যক্ষদর্শীদের সবচেয়ে বিস্ময়কর লাগে। দ্বিতীয় রাইখের বিপর্যয় তাদের উদ্ভ্রান্ত করেছিল যারা এটাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত এবং এর পতনকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছিল। কারণ এ রাইখ এত উঁচু জায়গা থেকে অবরোহণ করে যা কল্পনাতেও আনা যায় না। আর এ পতন জাতি এবং দেশের চরম দুর্দশা আর লাঞ্ছনা ডেকে এনেছিল।
দ্বিতীয় রাইখের প্রভা এত উজ্জ্বল আর প্রখর ছিল যে সমগ্র জাতি এ জন্য গৌরববোধ করত। পর পর অনেক অসমতল যুদ্ধ জয়ের পর, সম্রাট সেইসব যুদ্ধ বিজয়ী নায়কদের পুত্র এবং প্রপৌত্রদের হাতে এমন এক পুরস্কার তুলে দিয়েছিলেন, যা অকল্পনীয়। তারা অবশ্য এ বিষয়ে সচেতন বা অচেতন ছিল সেটা কোন কাজের কথা নয়। যাই হোক সমগ্র জার্মান জাতি এটা অনুভব করত যে এ পুরস্কার ধারাবাহিকভাবে কতগুলো আলোচনার মাধ্যমে আসেনি। এ রাষ্ট্রের সংস্থাপনা হয়েছে অন্যভাবে, যা নাকি আলোচনার মাধ্যমের চেয়ে অনেক মহৎ। এ রাষ্ট্রের যখন ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়, তখন সংসদীয় গুণশুনানির মধুর সঙ্গীত একে সঙ্গ দেয়নি। বরং প্যারীকে ঘিরে যে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছিল, সেই সঙ্গীতের মধ্যেই হয়েছে এর অভিষেক। এ পথ বেয়েই রাষ্ট্রনেতারা অভ্যর্থিত হয়েছিল সমগ্র জাতির কাছে। ভবিষ্যত রাইখেরও প্রতিষ্ঠা এখানেই। এর মাধ্যমেই রাজকীয় মুকুট মাথায় উঠেছিল। বিসমার্কের রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়নি কতগুলো বিশ্বাসঘাতক আর কর্তব্যে অবহেলা করা লোকের দ্বারা। এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সত্যিকারের সৈনিক দিয়ে–যারা রক্ত ঢেলে সীমান্তে সংগ্রাম করেছে। এ অবাক করা জন্য এবং পবিত্রতার দীক্ষিত আগুন দ্বিতীয় সম্রাট সম্পর্কে ধর্মান্ধে আত্মবিসর্জনকারী ব্যক্তি স্বর্গীয় মুকুট তুলে দিয়েছিল, যার ঐতিহাসিক গৌরব অল্প কয়েকটা পুরনো রাষ্ট্রেরই অধিকারে ছিল।
কী তীব্র গতিতে এ আরোহণ ক্রিয়া শুরু হয়েছিল। স্বাধিনতা দেশের মধ্যে জীবিকার গ্যারান্টি দিয়েছিল। জাতি লোকসংখ্যার দিক থেকেও বেড়ে চলেছিল এবং জাগতিক সম্পদেরও সমৃদ্ধি হচ্ছিল। রাষ্ট্রের সম্মানের সঙ্গে সঙ্গে জাতির সম্মানেরও নিরাপত্তা ছিল এবং সৈন্যবাহিনীর দ্বারা তা সুরক্ষিত ছিল; এটাই ছিল নতুন রাইখ আর পুরনো জার্মান জাতির পার্থক্য।
কিন্তু দ্বিতীয় সম্রাটের এবং জার্মান জাতির পতন এত সুগভীর হয়েছিল যে সবাই একেবারে হতবুদ্ধি অবস্থায় গিয়ে পৌঁছেছিল। এবং যার অবশ্যম্ভাবী প্রতিচ্ছায়া জনসাধারণের চোখে ধরা দিয়েছিল। সবকিছু দেখে মনে হয় সম্রাট এত উঁচুতে গিয়ে পৌঁছেছিল যে সাধারণ লোকে তা চিন্তার মধ্যেই আনতে পারেনি। বর্তমান দিনের তুলনায় গৌরবের সেই দিনগুলো কাল্পনিক এবং অবাস্তব বলেই মনে হয়। এসব মনে রাখলে আমরা বুঝতে পারব কেন লোকেরা এত হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। যখন তারা সম্ভ্রমের সঙ্গে অতীতটাকে চিন্তা করত, তখন পতনের লক্ষণগুলো নিশ্চয়ই তাদের নজর এড়িয়ে গেছে, যেগুলো নিশ্চয়ই কোন একপ্রকার অবয়বে ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে উপস্থিত ছিল। অবশ্যই এ কথাগুলো তাদের ক্ষেত্রে সত্য, জার্মানি যাদের কাছে শুধুমাত্র বাসস্থান বা জীবিকা আহরণের ক্ষেত্রমাত্র ছিল না। তাদের পক্ষেই একমাত্র বর্তমান অবস্থা প্রাকৃতিক বিপর্যয় বলে বোধ হবে। আর অন্যদের চোখে এটা হবে নীরবে এতদিন ধরে তারা যে ইচ্ছে করে এসেছে, সেই ইচ্ছাপূরণ।
ভবিষ্যতের বিপর্যয়ের লক্ষণ বলে নিশ্চয়ই সেই দিনগুলোতে অনুভূত হয়েছে, যদিও খুবই অল্প সংখ্যক লোক এ রহস্যভেদের চেষ্টা করেছে। কিন্তু বর্তমানে অন্যকিছুর চেয়ে সেই লক্ষণগুলোই খুঁজে বার করার অত্যধিক প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। শারীরিক রোগ নির্ণয় যেমন তখনই সম্ভব, যখন তার লক্ষণগুলো ধরা যায়; তেমনি রাজনীতির ক্ষেত্রেও এটা একই রকমের সত্য। বাইরের ফুটে ওঠা রোগের কারণগুলো খুঁজে বার করা ভেতরের কারণগুলোর থেকে যেমন সহজ, কারণ সেগুলো সোজাসুজি চোখকেআকর্ষণ করে। এ কারণেই অনেকে বাইরের লক্ষণগুলো দেখে রোগ নির্ণয়ে ব্রতী হয়েছিল। এবং বলাবাহুল্য তারা ব্যর্থও যে হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সত্যি বলতে কি অনেক সময়েই তারা চেষ্টা করে এ অন্তনিহিত কারণগুলোর অস্তিত্ব এড়িয়ে যেতে। এবং এ কারণেই আমাদের মধ্যে বেশির ভাগ লোক অর্থনৈতিক দুর্দশাই এ পতনের মূল কারণ বলে ধরে নিয়েছিল। প্রত্যেকেই তার অংশের দায়টুকু বহন করতে হয়েছে এবং সেই কারণে অর্থনৈতিক দুর্ঘটনাই বর্তমানের শোচনীয় অবস্থার জন্য দায়ী বলে ভেবেছে। সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং নৈতিক অধঃপতনই এ বিপর্যয়ের কারণ। অনেকেরই এ দুই জিনিস বোঝার ক্ষমতা অর্থাৎ প্রয়োজনীয় অনুভূতি এবং বোঝার মত জ্ঞান থাকে না।
এ জন্যই জার্মানির পতনকে জনসাধারণের বিরাট গোষ্ঠী কিসের জন্য মেনে নিয়েছিল তা বোঝা যায়। কিন্তু এর চেয়ে সত্য হল বুদ্ধিমান গোষ্ঠীও জার্মানির এ পতনের কারণ অর্থনৈতিক বিপর্যয় বলে ধরে নিয়েছিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা ধারণা করেছিল এর আরোগ্য সম্ভব একমাত্র অর্থনৈতিক উন্নতিতে। আমার মতে এ কারণেই জার্মানির কোনরকম উন্নতি সাধিত হয়নি। কোন উন্নতিই সম্ভব নয় যতক্ষণ না জাতি বুঝতে পারছে যে অর্থনৈতিক চেতনা জাতির উন্নতির দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের বিষয়। এবং জাতির উন্নতির মূল কারণ হল রাজনৈতিক, নৈতিকতা এবং সম্প্রদায়গত কারণগুলো। একমাত্র বর্তমানের শয়তানগুলোকে বোঝা সম্ভব, যখন এ কারণগুলো উপলব্ধি করা যাবে এবং তখনই তার রোগ নিরাময়ের প্রতিশোধের ও খুঁজে বার করা সম্ভব হবে।
সুতরাং জার্মানির পতনের রহস্যটা ভেদ করা অতীব প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে এ বিপর্যয়কে যদি অতিক্রম করতে রাজনৈতিক কোন আন্দোলন আরম্ভ করতে হয়, তবে এটা জানা থাকা তো অতি আবশ্যক।
জার্মানির টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়ার কারণ খুঁজতে গিয়ে অতীতকে বিশ্লেষণ করার সময় সতর্ক থাকার প্রয়োজন এ কারণে যে বাইরের রোগের লক্ষণগুলো যেন আমাদের প্রতারণা করতে না পারে। কারণ সেগুলোই আমাদের চোখে প্রথমে ধরা পড়ে অব্যক্ত কারণগুলোকে আমাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রাখবে।
অত্যন্ত সহজবোধ্য বলে এবং সেই কারণে বেশিরভাগ লোকের বর্তমানের দুর্দশা মেনে নেওয়া কারণগুলো হল যুদ্ধে পরাজয়। এবং সত্যি বলতে কি এটাই বর্তমান দুর্ভাগ্যের মূল কারণ। সম্ভবত অনেকেই এটা মনপ্রাণ থেকে বিশ্বাস করে থাকে। আবার অনেকে সচেতন মনে এবং ইচ্ছে করে মিথ্যা জেনেও বিশ্বাস করার ভাণ করে। বিশেষ করে সরকারি ঢাকনাবিহীন ভাণ্ডার যারা লুটে খাচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে এটা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বিপ্লবের অবতারণা বারে বারে জনতাকে বুঝিয়েছে যে যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক না কেন, জনসাধারণের কাছে তার কোন মূল্য নেই। উপরন্তু তারা এক হয়ে বলেছে ধনীরা হল এ মহাযুদ্ধের জয়লাভের স্বপক্ষে। সাধারণ জার্মান নাগরিক এবং শ্রমিক শ্রেণীর কোন উৎসাহ-ই নেই এ ব্যাপারে, যুদ্ধের ফলাফল যাহোক না কেন। সত্যি করে বলতে গেলে, এ অবতাররা নিশ্চিত হয়ে বলেছে যে জার্মানির পতনের কোন সম্ভাবনা নেই, বরং উন্নতির সম্ভাবনাই সমধিক। একবার যদি সামরিক ব্যবস্থা ভেঙে দেওয়া যায় তবে জার্মানির পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। এ চক্র কি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে মৈত্রীর গানে চারিদিক মুখরিত করে এ রক্ত পিপাসু যুদ্ধের অপরাধ জার্মানির কাঁধে চাপিয়ে দেয়নি? এ ব্যাখ্যা ছাড়া কি তারা এ তত্ত্ব প্রকাশ করতে পারত যে সাময়িক পরাজয়ের কোন প্রতিক্রিয়া রাজনৈতিক জগতে দেখা দেবে না, বিশেষ করে জার্মানদের ক্ষেত্রে? পুরো বিপ্লবটাকে কি ভোজ পানোৎসবে পরিণত করে জার্মানদের অগ্রগতি ব্যাহত করা হয়নি, যাতে স্বদেশে এবং বিদেশে জার্মানি বিজয়ীর সম্মান না পায়। মিথ্যাবাদী প্রতারকের দল, এটা কি সত্যি বলিনি?
এ ধরনের ধৃষ্টতা যা নিছক ইহুদী সৈন্যদের পরাজয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল, এবং তা-ই হল জার্মানদের পরাজয়ের কারণ। বাস্তবিকপক্ষে বার্লিন ভোরওয়ার্থ ছিল রাজদ্রোহের প্রধান হোতা; তারাই সে সময়ে লিখেছিল যে জার্মান সৈন্যদের বিজয়ী হয়ে দেশে ফিরতে দেওয়া হবে না। এবং এসব সত্ত্বেও তারা আমাদের সামরিক পরাজয়ের জন্য দোষারোপ করে।
এ সব মিথ্যাবাদীদের সঙ্গে কোনরকম বিতর্কে যাওয়া অনর্থক। যারা এ মুহূর্তে যা বলে পরের মুহূর্তেই তা অস্বীকার করে। এদের সম্পর্কে আমি আর কোন শব্দ ব্যয় করব না। কারণ তোতা পাখির মত অনেক চিন্তাহীন লোক আছে যাদের এটাই হল কাজ। এবং যারা এ কাজ করবে কোন খারাপ মতলব ছাড়াই। কিন্তু আমি যে পর্যবেক্ষণ করেছি তা হল আমাদের সগ্রামীদের জন্য; কারণ তারা তো কার্যক্ষেত্রে দেখতে পারে এ মুহূর্তে যা বলছে, পরের মুহূর্তেই তা ভুলছে এবং নিজের মত করে সেই কথাটা ঘোরাচ্ছে।
যুদ্ধে পরাজয়ই যে জার্মানির পতনের কারণ তার উত্তর ঠিক মত নিচে দেওয়া হল।
এটা সত্যি যে যুদ্ধে পরাজয় জার্মানির ভবিষ্যতের ওপর দুঃখজনক বিরাট একটা আঘাত হেনেছিল। কিন্তু যুদ্ধে পরাজয়টাই এর একমাত্র কারণ নয়। বরং অন্য কারণের ফলাফল হল এটা। এ জীবন মৃত্যু সংগ্রামের বিপর্যয়কর সমাপ্তি হল আকস্মিক ট্রেন দুর্ঘটনার মত; সুতরাং যাদের স্বচ্ছ এবং সোজাসুজি চিন্তাক্ষমতা আছে, তাদের পক্ষে ব্যাপারটা বোধগম্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তেমন লোকও বর্তমান ছিল, যারা সেই ভয়ানক মুহূর্তে তাদের চিন্তাক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে ফেলেছিল। এবং বাকিরা প্রথমে সত্যটাকে বোঝার চেষ্টা করেছে, তারপর পুরো ব্যাপারটাকে অস্বীকার করে বসেছে। অন্যান্যরা তাদের গুপ্ত বাসনা চরিতার্থের পর বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে দেখেছে যে পুরো ব্যাপারটাই ঘটেছে তাদের যৌথ সম্মেলনে। এরাই হল এ বিপর্যয়ের জন্য দায়ী। এবং যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যই কারণ নয়। যদিও তারা এখন সমস্ত বিপর্যয়ের জন্য যুদ্ধ পরাজয়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিচ্ছে। সত্যি বলতে কি, তাদের কার্যের ফলাফল হল যুদ্ধে পরাজয়। এবং তাদের বর্তমানে দোষারোপের কেন্দ্র খারাপ নেতৃত্ব মোটেই এর জন্য দায়ী নয়। আমাদের শত্রুরা একেবারেই কাপুরুষ ছিল না। তারা এটাও জানত কি করে বীরের মতন মৃত্যুবরণ করতে হয়। যুদ্ধ শুরু হওয়ার প্রথম দিনেই তারা জার্মানিকে পিছু হটিয়ে দিয়েছিল; দুনিয়ার অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা এবং গুদাম তাদের ব্যবহারের জন্য মজুদ ছিল; যার দ্বারা সাময়িক ক্ষয়ক্ষতি তৎক্ষণাৎ পূরণ করা যায়। বাস্তবিক পক্ষে সারা পৃথিবী স্বীকার করে নিয়েছে যে সুদীর্ঘ চার বছর ধরে জার্মানির জয় সমানুপাত হারে সম্ভব হয়েছে একমাত্র নেতৃত্বের দরুণ, সৈন্যদের বীরত্ব তো এর সঙ্গে আছেই। যা কিছু কমতি ছিল তা পূরণ করা কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়; এবং তা-ই স্বাভাবিক। তাই সেই সৈন্যদের বিপর্যয় আমাদের দুর্দশার কারণ নয়। এটা হল অন্য দোষগুলোর ফলাফল। এবং এগুলোই পতনটাকে আরো গভীরে টেনে নামিয়েছে; যা খোলা চোখে স্পষ্ট দেখা সম্ভব। এ সত্যিকারের কারণগুলো নিচে এভাবে দেখানো যেতে পারে :
সামরিক পরাজয় কি জাতি এবং দেশকে এভাবে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারে? যখন এটা দুর্ভাগ্যজনক কোন দুঃখের ফলাফল হয়? বাস্তবিকপক্ষে একটা যুদ্ধে পরাজয়ের জন্য কি একটা জাতি ধ্বংস হয় এবং সেটাই কি একমাত্র কারণ হতে পারে?
এর উত্তর সংক্ষেপে দিতে গেলে বলতে হয়, অন্তদেশীয় ক্ষয়ই সামরিক পরাজয়ের কারণ। এবং তার সঙ্গে কাপুরুষতা, চরিত্রহীনতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা তো আছেই। এ কারণগুলো যদি সামরিক পরাজয়ের কারণ না হয়, তবে সামরিক পরাজয় জাতির পুনরুত্থানের সাহায্য করে এবং জাতিকে উন্নতির ওপরে স্তরে ক্ষেপন করে। সামরিক পরাজয় জাতির জীবনে কবরের স্মৃতি নয়। ইতিহাস খুঁজলে এ কথার যথার্থতার উদাহরণ প্রচুর পাওয়া যাবে।
দুর্ভাগ্যজনকভাবে জার্মানির সামরিক পরাজয় আকস্মিক কোন দুর্ঘটনা নয়। এটা হল চিন্তা-ভাবনা করে পাওয়া শাস্তি যা হল গিয়ে এ ব্যাপারের চিরন্তন প্রতিদান। এ পরাজয়ের আমাদের প্রয়োজন ছিল। কারণ এটা বাইরের কারণগুলো ত্যাগ করে ভেতরের কারণগুলোকে বিশ্লেষণ করতে শেখাবে। যদিও তারা প্রত্যক্ষ, কিন্তু বেশিরভাগ লোকই তা স্বীকার করে নেয়নি। যারা উটপাখির পন্থা অবলম্বন করেছে, যা দেখতে চায় শুধুমাত্র সেটাই দেখেছে।
জার্মানির লোকেরা যখন এ পরাজয় মেনে নিয়েছিল তখন যে লক্ষণগুলো জার্মানির গণজীবনে ফুটে উঠেছিল, আমরা এবার সেগুলোকে পরীক্ষা করে দেখি। এটা কি সত্যি নয় যে অনেকেই পিতৃভূমির এ দুর্বাগ্যে লজ্জাজনকভাবে উস্ফুল্ল হয়ে উঠেছিল? যদি তাদের ইচ্ছায় এ প্রতিশোধ না নেওয়া হয়ে থাকে, তবে এ ব্যাপারে কে এত উৎসাহী হবে? তেমন লোকও কি তাদের মধ্যে ছিল না, যারা এ বলে অহংকার করত যে তারাই সীমান্তকে দুর্বল করে দিয়ে জার্মানির এ বিপর্যয় ডেকে আনতে সাহায্য করেছে। সুতরাং শত্রুরা এ অসম্মান আমাদের কাঁধের ওপর চাপিয়ে দেয়নি, বরং আমাদের দেশবাসীই তা ডেকে এনেছে। তার জন্য যদি তারা পরে দুর্ভোগ বহন করে, তবে তা কি অনুপযুক্ত। পৃথিবীর ইতিহাস মন্থন করলেও কি এমন একটা দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে, যেখানে দেশবাসী নিজেরাই নিজেদের যুদ্ধপরাধী বলে গণ্য করেছে–সজ্ঞানে এবং ব্যাপারটা সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও!
না, এর আর পুনরাবৃত্তি নয়। যেভাবে জার্মান জাতি এ পরাজয়বরণ করেছে, আমাদের কাছে এটা প্রত্যক্ষ যে সত্যিকারের কারণ অন্য কোথাও সামরিক পরাজয়ের দরুণ কয়েকটা সীমান্ত হারানো বা আত্মরক্ষা না করতে পারা নিশ্চয়ই নয়। যদি সীমান্ত হারানোর জন্য এ বিপর্যয় আসত, তবে জার্মান জাতি তা সম্পূর্ণরূপে অন্যভাবে ব্যাপারটাকে গ্রহণ করত। তারা এই দুর্ভাগ্যকে দৃঢ়ভাবে দাঁতে চেপে থাকত, অথবা দুঃখে ভারাক্রান্ত অবস্থায় ভেঙে পড়ত। শত্রুর বিরুদ্ধে বিদ্বেষে এবং উন্নত্ততায় তাদের হৃদয় ভরে উঠত। হঠাৎ ঘটনার প্রবাহে অথবা ভাগ্যের আদেশে যাদের কপালে বিজয় তিলক পড়েছে, এবং সেক্ষেত্রে জাতি রোমের ব্যবস্থাপক সভার* অনুসরণে পরাজিত সৈন্যদের বরণ করত ও তাদের ধন্যবাদ জানাত উৎসৰ্গতার জন্য। এবং আরো অনুরোধ জানাত সম্রাটের প্রতি যেন তারা আনুগত্যতা না হারায়। এমন কি শর্তহীন আত্মসমর্পণও স্বাক্ষরিত হত আন্দোলিত না হয়ে স্থিরভাবে, যখন হৃদয় মথিত হত চরম প্রতিহিংসার তাড়নায়।
এ হল সামরিক পরাজয়ের সত্যিকারের অভ্যর্থনার নমুনা, যা নাকি ভাগ্যের আদেশে আরোপিত; যেখানে উল্লাস বা নাচ গানের অবকাশ থাকত না। থাকত না কাপুরুষদের অহংকার, আর পরাজিতদের সম্মান দেখানোর তো কোন প্রশ্নই আসে না। সীমান্ত ফেরা সৈন্যদের উপহাস করাও হত না। এবং তাদের মানসম্মানও ধূলায় ছুঁড়ে ফেলা হত না। কিন্তু সবচেয়ে বড় হল, সেই লজ্জাকর পরিস্থিতি বৃটিশ অফিসার কর্নেল রেপিংটনকে প্রবৃত্ত করত না জার্মানির প্রতি উপেক্ষামিশ্রিত অবজ্ঞা ছুঁড়ে দিয়ে বলতে, যে প্রতি তিনজন জার্মানের একজন হল বিশ্বাসঘাতক। না, এক্ষেত্রে এ রোগ প্রকৃত বন্যার রূপ কিছুতেই নিতে পারত না; যার জন্য গত পাঁচবছর ধরে বহির্জগতের কাছে প্রতিটি সম্মানের পদচিহ্ন মুছে গেছে।
এটা পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে জার্মানি টুকরো হয়ে যাওয়ার জন্যই যে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল তা কত বড় মিথ্যা। সামরিক পরাজয় হয়েছিল ধারাবাহিক ঘটনাগুলোর দ্বারা সৃষ্ট ব্যাধির জন্য এবং যার সক্রিয়তা যুদ্ধের পূর্বেই জার্মান জাতির গায়ে ফুটে ওঠে। এ যুদ্ধকেই আকস্মিক দূর্ঘটনা বলা চলে, যা দিবালোকের মত লোকের চোখে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছিল যে ব্যক্তিগত এবং জাতীয় জীবনে নৈতিকতা কতখানি বিষ বাষ্পের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন এবং আত্মরক্ষণতার অধঃপতন হয়েছে। এগুলোই হল প্রাথমিক কারণ যা নাকি বহুদিন ধরেই জাতির এবং সম্রাটের ভেতরে গোড়ায় সুড়ঙ্গ কেটে চলেছে।
কিন্তু ইহুদীরা তাদের মিথ্যা এবং সংগ্রামশীল সহকর্মীদের নিয়েই পড়ে থাকে। মার্কসবাদীরা সমস্ত দোষ সেই লোকটার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়, যে একা অতি মানবের লৌহ কঠিন ইচ্ছা এবং অদম্য উৎসাহ নিয়ে জাতিকে সেই দুর্ঘটনা এবং লজ্জাকর পরিস্থিতির হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিল। মহাযুদ্ধের পরাজয়ের দায়ভাগ লুডেনৰ্ডফের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে তারা নৈতিক অস্ত্রটা (যা নাকি শত্রুদের পক্ষে বিপদজনক) দূরে সরিয়ে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকদের পিতৃভূমির প্রতি বিচারের পথ প্রশস্ত করে দেয়। ওসবগুলোর পেছনের উদ্দেশ্যটা হল–যেটা সর্বতভাবে সত্য, যদিও এটা হল একটা বিরাট বড় মিথ্যা যে পেছনে একটা মহৎ শক্তি কাজ করে যাচ্ছে। কারণ সাধারণ জনতার বিরাট একটা অংশকে তাদের অনুভূতির স্তরকে ভুল বোঝানো সম্ভব, কিন্তু তা সচেতনে বা সজ্ঞানে সম্ভব নয়। সুতরাং তাদের এ মানসিক অবস্থাতে তারা বিরাট মিথ্যার কাছে যত সহজে বলি হয়, ছোটখাটো মিথ্যার কাছে ততটা নয়। কারণ জীবনের প্রসঙ্গে তারা ছোটোখাটো মিথ্যা বলেই থাকে। কিন্তু তাদের জীবনে বড় মিথ্যার কোন স্থান নেই। প্রকাণ্ড মিথ্যা তাদের কাছে মাথা তুলতেও সক্ষম হয় না, এবং তাদের পক্ষে একটা অবিশ্বাস্য যে অন্য কেউ সত্যটাকে বিকৃত করার ধৃষ্টতা রাখে। তাদের মন সব সময়ই সন্দেহের দোলায় দোলে যে এর পেছনে নিশ্চয়ই অন্য কোন ব্যাখ্যা আছে। বিরাট মিথ্যা সব সময় পেছনে একটা ছাপ রেখে যায়। এবং সেই ছাপ মুছে ফেলে দিলেও নিশ্চিহ্ন হয় না; এটা পৃথিবীর সমস্ত মিথ্যাবাদী বিশেষজ্ঞদের জানা। বিশেষ করে মিথ্যার বেসাতি নিয়ে যাদের নিত্য ঘরসংসার, তারা ভাল করেই জানে কি করে মিথ্যাটাকে জঘন্যতম উপায়ে ব্যবহার করতে হয়।
স্মরণাতীত কাল হতে ইহুদীরা অন্যান্যদের থেকে খুব ভাল করে জানে কি করে মিথ্যা এবং মিথ্যা অপবাদকে চরমভাবে কাজে লাগাতে হয়। তাদের নিজেদের অস্তিত্বই কি চরম মিথ্যার ওপরে নয়? বলা হয়ে থাকে তারা ধর্মীয় জাতি। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে দেখতে গেলে আদৌ কি ইহুদীরা একটা জাতি? এবং তা যদি সত্য হয় তবে কি জাতি? মানবজাতি যে মহান চিন্তানায়কের জন্ম দিয়েছিল ইহুদীদের সম্পর্কে তার বিবৃতি সর্বাংশে সত্য। সোপেনহাওয়ার ইহুদীদের বলত মিথ্যাবাদীর চরম শুরু। যারা এ বিবৃতির সত্যাসত্য দিকটাকে অনুধাবন করে না বা বিশ্বাস করতে চায় না, তাদের পক্ষে সত্য প্রতিষ্ঠা করা কিছুতেই সম্ভব নয়।
আমাদের জার্মান জাতির পরম সৌভাগ্য বলব যে এ চরম দুর্দশার দিনগুলোর হঠাৎ ঘটনাচক্রে ছেদ পড়ে এবং তা ভয়ানক বিপর্যয়ে পরিবর্তিত হয়। যদি ব্যাপারটা ধীর গতিতে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলত, আস্তে হলেও জাতি নিশ্চিত ধ্বংসের গর্ভে নিক্ষেপিত হত। রোগটাও হত দীর্ঘস্থায়ী; যেখানে রোগটা কঠিন হওয়াতে বাইরের সবার চোখে ধরা পড়ে গেছে; এটা কোন দুর্ঘটনা নয় যে মানুষ কালো প্লেগ রাজরোগের চেয়ে তাড়াতাড়ি নিরাময় করতে শিখেছে। কারণ প্রথমটা মৃত্যুর ভয়াল রূপ ধরে আসে, যা দেখে সমগ্র মানবজাতি শিউরে উঠে; আর অন্যটি আসে কপটতার ভাণ করে। প্রথমটা চরম ভয় ধরিয়ে দেয়, অন্যটা ভেতরে গোপনে কাজ করে চলে। ফলাফল হল, মানুষ প্রথমটার বিরুদ্ধে ভয়ানকভাবে ভয় পেয়ে গিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করে, অপরদিকে রাজরোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যবস্থা অনেক দুর্বলতার। এভাবে মানুষ প্লেগকে নির্মূল করতে সক্ষম হলেও রাজরোগ নির্মূল করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি।
জাতির জীবনে রোগের ক্ষেত্রেও এটা সর্বাংশে সত্য। যতদিন না পর্যন্ত এ রোগ বিপর্যয়-স্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়, জনসাধারণ এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে বশবর্তী হয়ে যায়। তখন ভাগ্যের একটা ধাক্কায়, যদিও সেটা তিক্ত–ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয় ধীর গতিতে তা হ্রাস পাবে, নাকি বলির জন্য উৎসর্গীকৃত মানুষগুলোকে সেই রোগের শেষ পর্যায়ে এনে দাঁড় করাবে। বেশির ভাগ এ আকস্মিক দুর্ঘটনা তৎক্ষণাৎ সারানো না গেলেও দীর্ঘদিন ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়।
কিন্তু এক্ষেত্রেও সর্বপ্রথমে প্রয়োজন ভেতরকার গুপ্ত কারণটাকে টেনে বার করা যা থেকে এ রোগের উৎপত্তি।
সবচেয়ে প্রয়োজনীয় প্রশ্নটা হল মূল কারণ থেকে যে পরিবেশে এটা বেড়ে উঠেছে তাকে আলাদা করা। আর যতদিন পর্যন্ত এ রোগের জীবাণু দেহে থেকে যায়, ততদিন পর্যন্ত এটাকে রোগ মুক্ত করা সত্যই কষ্টকর। দীর্ঘদিন ধরে থাকায় এটা দেহের একটা অঙ্গ বিশেষ হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময়েই দেখা যায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এ বিষাক্ত বীজ জাতির একটা অঙ্গে পরিণত হয়ে গেছে, তখন কিছুতেই এটাকে মুক্ত করা আর সম্ভব হয়ে ওঠে না। তখন এটাকে প্রয়োজনীয় একটা শয়তান বলে ধরে নেওয়া হয়। সুতরাং এ বিদেশী জীবাণু শরীরের ভেতর থেকে খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা থেকেই মানুষ বিরত থাকে।
যুদ্ধ পূর্বের দীর্ঘ শান্তির দিনগুলোতে এ শয়তানের উপস্থিতি নিশ্চয়ই ছিল। কি : একবার বা দুবারের বেশি তাদের খুঁজে বার করার কোন প্রচেষ্টাই হয়নি। এখানেও আবার সেই অর্থনৈতিক অবস্থাটাই নজরে এসেছে যা নাকি সহজে দৃশ্যমান। অপর যে শয়তানগুলো নীরবে দেহের অভ্যন্তরে আত্মগোপন করে আছে তার চেয়ে।
ক্ষয়রোগের অনেকগুলো চিহ্নই সেদিন বর্তমান ছিল যার ওপরে বিশেষভাবে চিন্তা করাটা উচিত ছিল। অর্থনৈতিক দুরবস্থা সম্পর্কে নিচের কথাগুলো বলা যায় :
যুদ্ধের আগে বিপুল পরিমাণে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক উন্নতির চেয়ে দৈনন্দিন রুটি জোগাড়ের সমস্যাটাই বড় হয়ে ওঠে; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যারা এজন্য দায়ী, তাদের মাথায় কিছুতেই সঠিক সমাধানটা আসে না; তাই তারা সস্তায় বাজীমাৎ করার রাস্তাটাই বেছে নেয়। নতুন সীমান্ত দখলের ধারণাটাকে পরিত্যাগ করে তার পরিবর্তে এদের ব্যবসার তালে দুনিয়া জয়ের প্রচেষ্টাটাকেই শেষমেষ ক্ষতিকারক শিল্পকেন্দ্রীক করে তুলেছিল।
তার সর্বপ্রথম এবং প্রধান ভয়াবহ ফলাফল হল কৃষিজীবী সম্প্রদায়কে দুর্বল করে দেওয়া।
ধনী এবং দরিদ্রের পার্থক্যটা এতই প্রকট হয়ে পড়ে যে সেটা চোখে পড়ার মত। বিলাসিতা এবং দারিদ্রতার এত ঘেঁষাঘেষি সহাবস্থান যে তার ফলাফল শোচনীয় হতে বাধ্য। অভাব এবং বেকারত্ব আশ্চর্যজনক খেলা দেখাতে শুরু করে, যার পরিণতি চরম অসন্তোষ এবং পরস্পরের তিক্ততায়। তার ফল হয় জনসাধারণ রাজনীতিতে বিভিন্নমুখী হয়ে পড়ে। ব্যবসায়িক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অসন্তোষও বেড়ে চলে। ব্যাপারটা এমন এক জায়গায় এসে ঠেকে যে আর চলতে পারে না, সকলেরই মনে এ ধারণাটা জন্মায়। যদিও কারোরই ধারণা ছিল না যে সত্যিকারের কি ঘটতে যাচ্ছে।
ছড়িয়ে থাকা অসন্তোষ যে জনজীবনে কত গভীরে পৌঁছেছিল এগুলোই হল তার। টিপিক্যাল এবং দৃশ্যমান চিহ্ন।
শিল্পই দেশকে চালনা করতে শুরু করে এবং অর্থ ঈশ্বরের জন্য নির্দিষ্ট জায়গাটা দখল করে এমনভাবে বসে যে তা দিয়ে শুধু যে যা ইচ্ছা করা সম্ভব তা নয়, সবাই তার কাছে মাথা নত করতেও বাধ্য হয়। স্বর্গের ঈশ্বর যেন পুরনো দিনের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায় এবং তাকে তার জায়গা কুবেরের জন্য ছেড়ে সরে দাঁড়াতে হয়। এভাবেই চরম অধঃপতনের দিন ঘনিয়ে আসে যা প্রকৃতই জাতির পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ তৎকালীন অবস্থা এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিল যখন জাতির ভাগ্যে প্রশংসাটা জোটা উচিত। কারণ দুঃসময়ের লগ্ন তখন ঘনায়মান। জার্মানির উচিত ছিল তরবারীর দ্বারা রুটি জোগাড় করা, যাতে সে তার প্রয়োজনীয় রুটি পেতে পারে।
দুর্ভাগ্যবশত অর্থের এ প্রাধান্য জাতির প্রত্যেক অংশের স্বীকৃতি পায়, যার বিরোধীতা করা একান্তভাবেই উচিত ছিল। মহামান্য কাইজার একটা ভুল করেছিল যখন তার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে এ সমস্ত কুবেরদের জায়গা করে দেয়। স্বীকৃতভাবে যদিও ক্ষমা চেয়েই বলতে বাধ্য হচ্ছি যে এমন কি বিসমার্ক পর্যন্ত এ ব্যাপারটার বিপদ বুঝতে সক্ষম হয়নি। বাস্তবে সব আদর্শগুলোকে অর্থের পরিমাপে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হয়। কারণ এটা তো পরিষ্কার যে এ রাস্তায় হাঁটতে অর্থের নিকট তরবারীর স্থান দ্বিতীয় পর্যায়ের।
অর্থনৈতিক বিলি ব্যবস্থা যুদ্ধে চেয়ে অনেক সহজ। সুতরাং কাছাকাছি ইহুদী ব্রাঙ্কের সংস্পর্শে আসা কোন সত্যিকারের বীর বা রাষ্ট্রনেতার পক্ষে আর আশ্চর্যের কি আছে! সত্যিকারের প্রতিভা কখনই সস্তা হাততালি চায় না; সুতরাং এটাই তো স্বাভাবিক যে সে তা’ ধন্যবাদের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করবে।
অর্থনৈতিক চরম সংকট ধীরে ধীরে ব্যক্তিগত স্বার্থটাকে বড় করে তুলে পুরো অর্থনীতিটাকেই যৌথবদ্ধ কোম্পানিগুলোর হাতে সঁপে দেয়।
এভাবে অসৎ প্রতারকদের হাতে শ্রমিকদের জীবনজুয়ার পাশা হয়ে পড়ে। ব্যক্তিগত সম্পদের মালিকানা ভয়াবহভাবে বেড়ে ওঠে। অর্থনৈতিকচক্র জয়ের পথে ঘোরে এবং ধীরে হলেও জাতীয় জীবন পরিচালিত করতে শুরু করে।
যুদ্ধের আগেই ঘোরাল পথে শেয়ার কেনাবেচায় জার্মান অর্থনীতির ওপর আন্তর্জাতিক স্পষ্ট ছাপ মেরে দিয়েছিল। এটা সত্যি যে কয়েকজন জার্মান শিল্পপতি বিপদের চাকাটা উল্টোভাবে ঘোরাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শেষমেষ যখন সমবেতভাবে অর্থনীতিকে কুক্ষিগত করার প্রচেষ্টা প্রবলতর হয়ে ওঠে মাকর্সবাদের কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরদের দ্বারা, তখন তারা একরকম বাধ্য হয়েই সরে আসে।
জার্মান ভারি শিল্পের ওপর ক্রমাগত যুদ্ধই হল মার্কসবাদীরা যে জার্মান অর্থনীতিকে আন্তর্জাতিকতার রূপ দিতে চেয়েছিল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু শেষে এটাকে সাফল্যের চরম পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠেনি যখন মার্কবাদীরা বিপ্লবে জেতে। এ কথাগুলো লেখার সময়ে, বিশেষ করে আমার মনে হয়েছে জার্মান রেলওয়ের ওপর যে আক্রমণ করা হয়েছিল, যা শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদীর খপ্পরে গিয়ে পড়ে। এভাবে ইন্টারন্যাশনাল সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি আবার তাদের লক্ষ্য পথে চূড়ান্তভাবে এগিয়ে চলে।
জার্মান জাতিকে কতখানি পরিমাণে বেনিয়া করে তোলা হয়েছিল, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল যুদ্ধ শেষে জার্মান শিল্পপতিদের একজন মন্তব্য করেছিল যে ব্যবসাই একমাত্র শক্তি যার দ্বারা আবার জার্মান জাতির পুনর্গঠন সম্ভব। এ অনর্থক কথাগুলো বলা হয়েছিল ফ্রান্স যখন মনুষ্যত্বের পরিমাপে লোক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে ব্যস্ত; এটা বলার অর্থ হল যে জাতীয় জীবনে আদর্শের চেয়ে টাকার মূল্য অনেক বেশি। স্টাইনস্ যা পৃথিবীব্যাপি রেডিওর মাধ্যমে বলেছিল তা এক চরম অবিশ্বাস্য সন্দেহের দোলায় পুরো জাতিকে দোলায়। মতামতটাকে তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করে তারা উদ্দেশ্যটাকে বাচাল এবং মতলববাজের দল প্রধান উদ্দেশ্য বলে ঘোষণা করতে শুরু করে–যে ভাগ্য রাষ্ট্রনেতাদের বিপ্লবের পরে জার্মানিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।
ক্ষয়িত জার্মানির সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল যুদ্ধের আগে কাজ অর্ধেক করার অভ্যাস। এর ফলাফল হল অনিশ্চিয়তা, যা জীবনের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। নির্দিষ্ট একটা কাপুরুষতাকে প্রশ্রয় দিয়ে ফলাফলে পৌঁছেছিল এক একটা কারণে। এবং শেষ পর্যন্ত এসব পীড়া শিক্ষাপদ্ধতিকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে।
প্রাক যুদ্ধের জার্মান শিক্ষা ব্যবস্থায় কতগুলো বিরাট গলতি ছিল। এক, সীমাবদ্ধতা ছিল পুরোপুরি জ্ঞান নির্ভর এবং প্রত্যক্ষ কাজে লাগতে পারে সেদিকে নজরই দেওয়া হয়নি। তার চেয়েও অনেক কম নজর দেওয়া হয়েছিল ব্যক্তিগত চরিত্র গড়ায়; যতখানি সম্ভব শিক্ষার এ বিশেষ দিকটাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিল। এবং দায়িত্বজ্ঞান, ইচ্ছাশক্তি ও বিচার ক্ষমতা বৃদ্ধির দিকে এ শিক্ষা একেবারেই সাহায্য করে না। তার ফলে যে সব লোক এ শিক্ষা ব্যবস্থায় তৈরি হয়, তারা হল আদবকায়দা আর ভাবাবেগ সর্বস্ব। যুদ্ধের আগে জার্মানদের আদব-কায়দা আর ভাবাবেগ সর্বজাত বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। জার্মানদের লোকে ভালবাসত কারণ তাদের ব্যবহার করা চলত বলে। কিন্তু তাদের চারিত্রিক এ দুর্বলতার দরুণ সম্মান বলতে কিছু পেত না। যাদের এ রহস্যের গভীরে যাওয়ার ক্ষমতা ছিল, তাদের মধ্যে একমাত্র জার্মানরাই সর্বপ্রথম তাদের জাতীয়তা ত্যাগ করে নিজ ভূমে পরদেশীর মত বসবাস করতে শুরু করে। এবং তখন সমস্ত পৃথিবীতে একটা কথা অতি প্রচলিত ছিল যে, একটা টুপি হাতে করে যে কেউ সমগ্র দেশটার মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে পারে।
এ ধরনের সামাজিক শিষ্টাচার বিপর্যয় ডেকে আনে, বিশেষ করে যখন নির্দেশ আসে মহামান্য রাজার উপস্থিতিতে কতগুলো বিশেষ শিষ্টাচার দেখাতে হবে। এ নির্দেশ হল আদব-কায়দা পরস্পর বিরোধী হতে পারব না, এবং মহামান্য সম্রাট যা পছন্দ করেন। সেই ধরনের আদব-কায়দাই মেনে চলতে হবে।
এটা হল পরিষ্কার ব্যাপার যে মর্যাদার মূল্য দিতে হবে, যে আদব-কায়দা শুধু লক্ষ্য সাধনের জন্য তা বরদাস্ত করা হবে না। সম্রাটের উপস্থিতিতে দাসের মত ব্যবহার হয়ত বা যথেষ্ট পরিমাণে উপযোগী, অবশ্যই পেশাগত দাসদের এবং জায়গা খোঁজার। লোকদের পক্ষে সত্যি বলতে কি এ ক্ষয়িষ্ণু জীবগুলোর পরিক্রমণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ওপরের স্তরে ব্যপ্ত; সাধারণ সৎ নাগরিকদের মধ্যে এদের ঘোরাফেরা নেই বললেই চলে। এ অতিশয় বিনীত জীবেরা তাদের প্রভু এবং রুটি জোগানোর কর্তার কাছে সাষ্টাঙ্গে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ত, কিন্তু অন্যদের কাছে তাদেরই ব্যবহার ছিল উদ্ধত, বিশেষ করে তাদের ধৃষ্টতা এত বেশি ছিল যে তারা একমাত্র নিজেদেরই মানুষ বলে জ্ঞান করত। এবং নিজেদের রাজকীয় মহিমা সম্পন্ন বলে ঘোষণা করতেও দ্বিধা ছিল না তাদের।
এ কাজগুলোর সাহায্যে তারা রাজার এবং রাজকীয় আদর্শগুলোর পতন ঘটাবার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে; এছাড়া আর কিছু হতে পারে না। একটা মানুষ যখন যে কোন পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে, তখন সে কখনই তাদের সামনে মাটিতে উপুড় হয়ে সাষ্টাঙ্গে ধুলোয় পড়ে তাকে প্রণাম করবে না। সে যদি কোন প্রতিষ্ঠানের সমৃদ্ধির জন্য সত্যিকারের শুভাকাক্ষী হয়, তবে সে কিছুতেই নিরুৎসাহ হবে না, কোন সদস্য সেই প্রতিষ্ঠানের দোষত্রুটি যতই দেখিয়ে তাকে নিরুৎসাহ করার চেষ্টা করুক না কেন। এবং এটাও সত্যি যে সে সারা পৃথিবী ঘুরে ঢাক পিটিয়ে এ বিষয় বলে বেড়াবে না, যা নাকি তথাকথিত গণতন্ত্রের কয়েকজন বন্ধু করে বেড়িয়েছে। তার পরিবর্তে সে তার রাজার কাছে আবেদন জানাবে, এবং সেই রাজার নিকট তার কাজ হল পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝিয়ে বলে সেভাবে কাজ করিয়ে নেওয়া। উপরন্তু তার পক্ষে এ ধরনের চিন্তাধারা গ্রহণ করা অনুচিত যে রাজা যা ভাল বুঝবে তাই করবে; এমন কি যদি তার নির্দেশিত পথ দেশ এবং জাতিকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। আমি যে মানুষের স্বপ্ন দেখি, তার কর্তব্য হল রাজার কার্যকলাপের বিরোধিতা করে হলেও প্রয়োজনে রাজকীয় ব্যবস্থাকে রক্ষা করা। রাজকাজ করতে গিয়ে ব্যক্তিগতভাবে তাকে যত বড় দায়িত্বের মুখোমুখি হতে হোক না কেন; যদি রাজকীয় প্রতিষ্ঠানগুলো রাজার কার্যকলাপের ওপরে নির্ভর করে, তবে এর চেয়ে শোচনীয় প্রতিষ্ঠান আর হতে পারে না। কারণ খুব কর্মক্ষেত্রেই আদর্শ রাজা জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতীক এবং পূর্ণ চরিত্রের লোক দেখা যায়, যদিও আমরা অন্যরকম চিন্তা-ভাবনা করতেই অভ্যস্ত। কিন্তু ওই সত্য পেশাগত জোচ্চর এবং গোলামদের কাছে স্বাদহীন ঠেকবে। তবু মাথা উঁচু করা সবাই, যারা হল একটা জাতির মেরুদণ্ড বিশেষ, জ্ঞানী এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি এ অর্থহীন বাচাল চিন্তাধারা ত্যাগ করে থাকে। কিন্তু যদি একটা জাতির সৌভাগ্য হয় মহান রাজ্য বা মহান কোন ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হবার, তবে এটা মেনে নিতেই হবে যে সমস্ত কিছুর ঊর্ধ্বে সেই জাতির সৌভাগ্যের তারা জ্বলজ্বল করছে; এবং তাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত যে খুব খারাপ অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য ভাগ্য তার প্রতিকূলে নয়।
এটা পরিষ্কার যে রাজকীয় আদর্শগুলোর মূল্যায়ন এবং স্বার্থকতা শুধু রাজার ওপরেই নির্ভরশীল নয়। অবশ্য যদি না সেই মুকুট স্বর্গের আদেশপ্রাপ্ত হয়ে বীর দ্য গ্রেট ফেডারিক বা বিচক্ষণ ব্যক্তি উইলিয়াম ফার্স্টের শিরে বসানো না হয়। এটা অবশ্য কয়েক শতাব্দীতে একবারই ঘটে থাকে। এর পুনরাবৃত্তি তার থেকে বেশি ঘটে না। রাজকীয়তার আদর্শ ব্যক্তির মানক্রমে হয়ে থাকে। অর্থাৎ মুকুটধারীর মানসিকতার উপরে নির্ভরশীল। আর প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপের ভেতরেই নিহিত থাকে। এভাবে রাজাও সেইসব দায়িত্বশীল লোকদের পর্যায়ে পড়ে যাদের কর্তব্যকর্ম হল প্রতিষ্ঠানের সেবা করা। রাজা পর্যন্ত এ যন্ত্রের চাকা বিশেষ এবং তাকেও তার কর্তব্যকর্ম করে যেতে হবে। সেই উঁচু আদর্শের পরিপূর্ণতার জন্য তারও একান্তভাবে কাজ করে যাওয়া উচিত। সুতরাং এ আদর্শের সঙ্গে এর অর্থ যদি জড়িত না থাকে তবে সমস্ত কিছুই সেই তথাকথিত পবিত্র ব্যক্তিত্বের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে। তখন আর সেই ক্ষীণ দুর্বল লোকের পক্ষে যোগ্যতার সঙ্গে শাসনকার্য পরিচালনা করা সম্ভব নয়।
বর্তমানে সেই সত্যযুগের ওপরে জোর দেওয়া উচিত, কারণ এখন সেইগুলোই আবার ফিরে এসেছে; এবং রাজকীয় ব্যবস্থা ধ্বংসের জন্য এগুলো খুব কম দায়ী নয়। বেশ কিছুটা ধৃষ্টতার সঙ্গে এ লোকগুলোই আবার তাদের রাজার কথা বলে; একেই তারা কয়েক বছর আগে নির্লজ্জের মত পরিত্যাগ করেছিল যখন তার সত্যিকারের সঙ্গীন সময় উপস্থিত। যারা এ মিথ্যে কথার কোরাসে নিজেদের গলা মেলায়নি, তাদেরই খারাপ জার্মান নামে অভিহিত করে ধিক্কার জানানো হয়েছে। যারা এ আখ্যা দিয়েছিল তারা হল ১৯১৮ সালের ন্যায় পলায়নবাদী এবং নিজেদের স্বার্থের তাগিদায় লাল ব্যাজ ধারণ করতে শুরু করে। তাদের চিন্তায় পরিণামদর্শিতা শৌর্যের চেয়ে অনেক শ্রেয়। কাইজারের কি ঘটছে তা নিয়ে তাদের মাথা ব্যাথা নেই। তারা এমন ভাণ করত যেন তারা শান্তিপূর্ণ নাগরিক; কিন্তু প্রায়ই দেখা যেত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তারা দল বেঁধে অদৃশ্য। হঠাৎ এ রাজমর্যাদার বাহকদের প্রয়োজনের সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। পরিবেশ অনুযায়ী এ দাসের দল এবং সদস্যরা একে একে আবার নাট্যমঞ্চে আবির্ভূত হয়, যাতে আবার তারা রাজার উদ্দেশ্যে জিহ্বা চালনা করতে পারে। অবশ্যই যখন অন্যান্য রাজার বিরোধিতা করার প্রয়াসকে দমন করে ফেলেছে। আবার তারা একত্রিত হয়ে মিশরের ভাল খাদ্যদ্রব্য ও স্বাচ্ছন্দ বিলাসের কথা স্মরণ করে। এবং রাজার আনুগত্যে বিভোর হয়ে পড়ে। ব্যাপারটা এ গতিতেই চলতে থাকে, যতদিন না পর্যন্ত লাল ব্যাজের দিন প্রবল হয়ে ওঠে। তখন আবার পুরনো ঝরঝরে সদস্যদের যারা রাজকীয় মহিমার গুণগানে মুখর পুনশ্চ কয়লা রাখার বদলী পাত্রের মত পলায়ন করে। ঠিক যেমন করে বিড়ালে মুখে করে ইঁদুর নিয়ে ছুটে পালায়।
যদি সম্রাট নিজে এসব ব্যাপারে দায়ী না হয় তবে প্রত্যেকেই তার প্রতি সহানুভুতি দেখবে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাদেরও উপলব্ধী করা উচিত যে তাদের সাহায্যে সিংহাসনই একমাত্র হারানো সম্ভব, ফিরে পাওয়া নয়।
এসব ভক্তি সম্ভ্রম হল আমাদের ভুল শিক্ষাপদ্ধতির ফলাফল, যা এ ক্ষেত্রে বিদ্বেষ বশে চরম শাস্তি দিয়েছিল। এ শোচনীয় সারবিহীন বস্তু জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত হয়ে রাজকীয় মর্যাদার গোড়ায় সুড়ঙ্গ কাটে। শেষ পর্যন্ত তা নড়ে চড়ে উঠলে সমস্ত কিছু তার গর্ভে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। স্বভাবতই জঘন্য এবং অতি নিচু তোষামোদকারী গলগ্রহরা কিছুতেই তাদের প্রভুর জন্য মরতে ইচ্ছুক ছিল না; রাজার পক্ষে এটা উপলব্ধী করা সম্ভব ছিল না এবং বুঝতে গেলে যতখানি কষ্ট সহ্যের প্রয়োজন, তার পক্ষে তত ক্লেশ বরণ করে নেওয়াটা অসম্ভব।
ভুল শিক্ষা পদ্ধতির একটা ভুল ফলাফল হল যা সততাই দৃশ্যমান তা কাঁধে দায়িত্ব নেওয়ার ভীতি এবং তার ফলপ্রাপ্তি হিসেবে অস্তিত্বসম্পন্ন মূল সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হওয়ার দুর্বলতা।
এ মড়কের শুরুর বিন্দু হল আমাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান, যেখানে বিশেষ করে দায়িত্ব বিমুখতা পরিপুষ্ট লাভ করে। দুর্ভাগ্যবশত ধীরে ধীরে এ অসুখ প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে; বিশেষ করে তা আঘাত হানে গণজীবনের ব্যাপারগুলোতে। সবদিক থেকেই দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দেওয়া হয়, যার জন্য প্রতিটি ব্যাপারেই আসে দোমনাভাব। ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধ প্রায় শূন্য হয়ে আসে।
আমরা যদি গণজীবনে বিভিন্ন সরকারের অনিষ্টকর ঘটমান বিষয়গুলোর বিচার বিবেচনা করে দেখি, তবে তৎক্ষণাৎ এ অর্ধেক হৃদয় দিয়ে দায়িত্ব নেবার কাপুরুষতার ভয়াবহ ফলাফল দেখতে পাব। অসংখ্য উদাহরণের মধ্যে আমি মাত্র কয়েকটা উদাহরণ এখানে পেশ করব।
সাংবাদিকচক্র রাষ্ট্রের মধ্যে সংবাদপত্রকে বিরাট একটা শক্তি বলে বর্ণনা করেছে।
সত্যি বলতে কি এর উপযোগীতা অসাধারণ। কারোর পক্ষে এটা সহজে হিসাব করা সম্ভব নয়। কারণ সংবাদপত্র শিক্ষা পদ্ধতির একটা দিক। এমন কি প্রাপ্তবয়স্কদের জীবনেও। বিশেষ করে সংবাদপত্র পাঠকদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, যারা যা কিছু পড়ে, তাতেই বিশ্বাস করে। দ্বিতীয়ত, যারা যা কিছু পড়ে, তারা কিছুতেই বিশ্বাস করে না। তৃতীয়দল হল, যারা পড়ে প্রচণ্ড সমালোচনার পর বিচার বিবেচনা অনুসারে সার বস্তুটি গ্রহণ করে। সংখ্যাতত্ত্বের দিক থেকে প্রথম দলটি অতি শক্তিশালী। কারণ গণসংখ্যার বেশির ভাগই এদের সমষ্টি। বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে জাতির তরফে এরা অত্যন্ত সহজ অংশের লোক। পেশাগত দিক থেকে পুরো জাতিটাকে ভাগ করা অসম্ভব; বরং বুদ্ধিমত্তার দিক থেকে এদের বাছবিচার করা যেতে পারে। এ পতাকার তলে তারাই জড়ো হয়, যারা শুধু নিজেদের চিন্তা-ভাবনা করার জন্য এ পৃথিবীতে আসেনি; অথবা যার এ শিক্ষা হয়নি কারণ এরজন্য কিছুটা তাদের অক্ষমতা এবং কিছুটা অজ্ঞতা; সেই কারণে তারা তাদের সামনে ছাপার অক্ষরে যে দেখে সেটাকেই বিশ্বাস করে বসে। এর মধ্যে আমরা সেই ধরনের অলসদেরও যোগ করব, যারা নিজেদের পরিপূর্ণ চিন্তা করার ক্ষমতা থাকা সত্বেও নেহাত আলসেমির জন্য অন্যের চিন্তাধারাটাকে গ্রহণ করে বিষয়গত এ ভেবে যে চিন্তাধারাগুলো পরিপূর্ণ। সুতরাং এ সবগুলোকে বিচার বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে সংবাদপত্রের প্রভাব জনজীবনে সুদূর প্রসারী। কারণ জনসাধারণের বিরাট একটা অংশের ওপর এ সংবাদপত্র প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কিন্তু যে কারণেই হোক অথবা অনিচ্ছুক বলে তারা এগুলোকে মানসিক চালুনি দ্বারা ঝেড়ে পার্থক্য করে না। সেই কারণে প্রাত্যহিক জীবনের সমস্যাগুলো হল এ স্বতন্ত্র প্রভাবের ফলাফল। গণজীবনের জ্ঞানলোক যদি সৎ চরিত্রের এবং দায়িত্ববোধ সম্পন্ন হয়, তবে এগুলোর একটা সুবিধাগত দিক আছে; কিন্তু যখন বদমায়েস এবং মিথ্যাবাদীরা এগুলোকে কাজে লাগায়, তখনই জাতির চরম ক্ষতি নেমে আসে।
সংখ্যার দিক থেকে দ্বিতীয় দলটি সত্যই ছোট। কারণ এর সমষ্টি হল প্রথম দলের যারা সারি সারি ঘটনা প্রবাহে তিক্ত হয়ে শেষমেষ ছাপার অক্ষরে যা দেখে তাকে অবিশ্বাস করে চলে। তারা সমস্তরকম সংবাদপত্রকে ঘৃণা করে থাকে। হয় তারা সংবাদপত্রে সবকিছু পড়ে না, অথবা বিষয়বস্তুর ওপরে তাদের চরম একটা রাগ থাকে। তারা সেগুলোকে মিথ্যার স্থূপ এবং ভুল বক্তব্য বলে ধরে নেয়। কারণ তাদের সবসময়েই সত্যের প্রতি একটা অবিশ্বাস থাকে। সেই কারণে কোন ইতিবাচক কাজকেই তারা অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করে।
তৃতীয় দলটি হল সত্যি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। কারণ সত্যিকারের বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন লোক দ্বারা এটা সৃষ্ট, যাদের স্বাভাবিক ধ্যান-ধারণা এবং শিক্ষা তাদের নিজেদের জন্যই চিন্তা করতে শেখায়, এবং এরা প্রতিটি বিষয়েই নিজেদের একটা মতামত খাড়া করতে সচেষ্ট হয়ে থাকে। তারা এমন কোন সংবাদপত্র পড়ে না যেখানে তাদের বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সংযোগকারী লেখকের বক্তব্যের মিল থাকে। এবং স্বভাবতই লেখকদের পক্ষে এটা খুব একটা সহজ কাজ নয়। সাংবাদিকরা এ ধরনের পাঠকদের বেশ কিছুটা পৃষ্ঠপোষকতাই করে থাকে।
সুতরাং এ কাজে সংবাদপত্রগুলোর বিপদজনক ক্ষমতা অতি অল্প, অপ্রয়োজনীয়ও বটে। বিশেষ করে তৃতীয় দলের সদস্যদের নিকট। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এ পাঠকবর্গ প্রত্যেক সাংবাদিককে অত্যন্ত অশ্রদ্ধার চোখে দেখে যারা কদাচ সত্য কথা বলে থাকে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হল এসব পাঠকবর্গের মূল্যায়ণ বুদ্ধিমত্তায়, তাদের সংখ্যার দ্বারা নয়, অসুখীজনক ব্যাপারটা হল সংখ্যাটাকেই গণনার মধ্যে ধরা হয়। বুদ্ধিমত্তাকে নয়। বর্তমান সময়ে যখন জনসাধারণের ক্ষেত্রে ভোটপত্রটাই কিছু স্থির করার মানদণ্ড, সেখানে পুরো ব্যাপারটাই হল গরিষ্ঠ সংখ্যা গোষ্ঠীর হাতে; অর্থাৎ প্রথম দলের। যারা নির্বোধ এবং সহজে বিশ্বাসী দলের লোক।
এটা হল একটা দেশের জাতীয় স্বার্থ যে এ দলটা যাতে কোন ধাপ্পাবাজের হাতে গিয়ে না পড়ে, যারা অজ্ঞ অথবা শয়তানি মতলবী কোন তথাকথিত শিক্ষক। সুতরাং রাষ্ট্রের কর্তব্য হল শিক্ষাপদ্ধতির উপর নজর রাখা যাতে এ ধরনের কোন অপরাধ সংগঠিত হতে না পারে।
বিশেষ করে সংবাদপত্রগুলোর ওপর যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে; কারণ এদের প্রভাব শুধু শক্তিশালীই নয়, সর্বব্যাপীও বটে। যেহেতু এর ফলাফল কিছু সময়ের জন্য নয়, বরং ক্রমাগত বলা চলে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নামে যা হোক করে ব্যাপারটাকে কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না, বা এ কর্তব্যে অবহেলা করাটাও সঙ্গত নয়। সমস্ত ব্যাপারটাই জাতির কাছে তুলে ধরা উচিত। কেন ভাল এবং কি করলে আরো ভাল হতে পারে তা বিশ্লেষণ প্রয়োজন। নির্দয়তার সঙ্গে রাষ্ট্রের উচিত শিক্ষা পদ্ধতির এ যন্ত্রটাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখা এবং জাতির ও দেশের সেবায় একে নিয়োজিত করা।
কিন্তু যুদ্ধ পূর্ব জার্মানিতে জার্মান সংবাদপত্রগুলো কি ধরনের খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করেছিল? এটা কি সবচেয়ে বিষাক্ত বিষ যা কল্পনায় আনা যায়। এটা কি বিশ্বজনীন শান্তিবাদের নিকৃষ্টরূপ নয় যা আমাদের দেশের লোকের ভেতরে ছুঁচের সাহায্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়নি? যখন অপরেরা ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতরূপে বাজপাখির ধারালো নখ দিয়ে জার্মান জাতির ওপরে ঝাপিয়ে পড়তে উদ্যত? এ সংবাদপত্রগুলোই শান্তির সময়ে বিন্দু বিন্দু করে সন্দেহের বীজ জনসাধারণের মনে ঢুকিয়ে দিয়েছে, যা নাকি আমাদের দেশের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। এভাবেই রাষ্ট্রের আত্মরক্ষার প্রচেষ্টার হাত দুটোয় হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছে। এ জার্মান সংবাদপত্রগুলোই আমাদের জনসাধারণের কাছে পরিবেশনা করেনি যে পশ্চিমী গণতন্ত্র কত বড় নিরর্থক? যতদিন পর্যন্ত না প্রচুর আগাছা তাদের ভবিষ্যত লীগ অব নেশানসের হাতে সুরক্ষিত বলে ভেবেছে? এ সংবাদপত্রগুলোই আমাদের লোকদের নৈতিক অধঃপতনের দিকে ঠেলে দিয়ে জনগণের সৌন্দর্য জ্ঞান এবং নৈতিকতাকে হাস্যস্পদের পর্যায়ে নিয়ে গেছে।
ক্রমাগত আক্রমণে সংবাদপত্রগুলো কি রাষ্ট্রের অধিকারের গোড়ায় সুড়ঙ্গ কাটেনি যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে একেবারে ধূলিসাৎ না করা যায়। সংবাদপত্রগুলো কি রাষ্ট্রের সম্পত্তি রাষ্ট্রকে দেওয়ার ব্যাপারে বারবার আপত্তি জানিয়ে আসেনি? ক্রমাগত সমালোচনায় সৈন্যদলের নাম-যশ টেনে নিচে নামিয়েছে, সাধারণের জ্ঞান বুদ্ধিকে পেছনে থেকে ছুরি মেরেছে এবং সামরিক বাহিনীর সুখ্যাতিকে অস্বীকার করেছে— যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের প্রচারকার্যে সফলতা এসেছে।
তথাকথিত এ সংবাদপত্রগুলোর কাজ ছিল জার্মান রাষ্ট্র এবং তার জনসাধারণের জন্য কবর খোঁড়া। মার্কসীয় সংবাদপত্রগুলোর মিথ্যার বেসাতি সম্পর্কে কিছুই বলা চলে না। তাদের কাছে বিড়ালের নিকট ইঁদুরের যেমন প্রয়োজন, মিথ্যা প্রচারটাও তাদের সেইরকম মূল আদর্শ। তাদের একমাত্র এবং সর্বপ্রধান কাজ ছিল জাতির মেরুদণ্ডটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করা, যাতে পুরো জাতটা আন্তর্জাতিক অর্থনীতির এবং তাদের প্রভু ইহুদীদের গোলাম হতে পারে।
জনগণের মনকে বিষাক্ত করে তোলার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রই বা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল?, কিছুই করেনি। এ নীতিতেই তারা ভেবেছিল এ মহামারীর হাত থেকে রেহাই পাবে। চাটুকারিতা আর সংবাদপত্রের মূল্যায়ণের অগ্রাধিকার স্বীকার করে। ইহুদীরা জেনেশুনেই মৃদু হেসে এগুলোকে স্বীকৃতি দিয়েছিল ধন্যবাদের সঙ্গে।
রাষ্ট্রের এ অসম্মানজনক ব্যর্থতার কারণ হল,–বিপদটাকে বুঝতে না পারা, তার চেয়ে বেশি হল কাপুরুষতার এবং ত্রুটিপূর্ণ অর্ধেক হৃদয় দিয়ে পুরো বিষয়টার মোকাবিলা করার। কারোর কোন মৌলিক এবং উৎসাহপূর্ণ পদ্ধতি ছিল না যার দ্বারা এর মোকাবিলা করা যেতে পারে। সবাই অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিয়েছে; অর্থাৎ এ পথ বেছে নিয়েছে। সোজাসুজি আঘাত করার পরিবর্তে বিষধর সাপকে খালি উত্তেজিতই করে তুলেছে। এর ফলাফল হয়েছে যে যেখানে ছিল সেখানেই পড়ে থেকেছে এবং এ প্রতিষ্ঠানের সংগ্রাম করার ক্ষমতা বছরের পর বছর বেড়েই গেছে।
যে ইহুদী সংবাদপত্রগুলো ধীরে ধীরে জাতিকে দুর্নীতির গ্রাসে জড়িয়ে ফেলেছিল তাদের বিরুদ্ধে তৎকালীন রাষ্ট্র যে আত্মরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল তাতে কোনরকম নির্দিষ্ট পন্থা ছিল না। এর পশ্চাতে যেমন সুনির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি ছিল না, তেমনি নির্দিষ্ট কোন বিষয়বস্তুও ছিল না যাকে অবলম্বন করে এ আত্মরক্ষামূলক প্রয়াস গড়ে তোলা যেতে পারে। আসলে পরিস্থিতিটাকে বুঝতেই তারা অসফল হয়েছে, যে কারণে সংগ্রামের গুরুত্ব, উপায় বা কোনরকম পরিকল্পনা করাই তাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। খালি সমস্যাটাকে নিয়ে টুং টাং শব্দ করেছে মাত্র। যখন কামড়টা জোরে বোধ হয়েছে, তখন এক আধজন সাংবাদিক বিষধর সর্পকে ধরে কয়েক সপ্তাহ বা মাসের জন্য জেলে পাঠিয়েছে; কিন্তু পুরো বিষের পাত্রটাকে শান্তিতে বয়ে নিয়ে যেতে দেওয়া হয়েছে।
এটাকে স্বীকার করে নিতেই হবে যে এটা হল একদিকে ইহুদীদের ধূর্তামীর ফল; অপরদিকে রাষ্ট্রের নির্বুদ্ধিতা এবং অকপট সরলতার পরিচয় মাত্র। ইহুদীরা চালাকির জন্য সংবাদপত্রগুলোর ওপরে সম্মিলিতভাবে এ আক্রমণ করতে দিয়েছিল। একে অন্যকে আচ্ছাদন দিতে চেষ্টা করেনি। অন্যদিকে গোপনীয় সমস্ত তথ্য মার্কসীয় সংবাদপত্রগুলো অত্যন্ত জঘন্য উপায়ে উদ্ঘাটিত করে সবার সামনে তুলে ধরেছিল, ভয়াবহরূপে সরকার এবং রাষ্ট্রকে আক্রমণ করেছিল এবং এক সম্প্রদায়কে অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। এ মধ্যবিত্তিক গণতান্ত্রিক সংবাদপত্রগুলোও ইহুদীদের হাতে ছিল এবং তারা ভালভাবেই জানত কি করে ছদ্মবেশ ধারণ করে সত্যিকারের বিষয়বস্তুটাকে লুকোতে হয়। তারা যত্নের সঙ্গে কর্কশ ভাষার ব্যবহার পরিত্যাগ করত; কারণ তারা জানত বোকারা ওপর ওপর দেখেই বিচারপৰ্ব সমাধা করে এবং সত্যিকারের কোন বিষয়বস্তুর গভীরে তারা প্রবেশ করতে পারে না। তারা বিষয়বস্তুর পরিমাপ করে বাইরের রূপটা দেখে। ভেতরে কি আছে তা দেখে না বা দেখার মত ক্ষমতাও তাদের নেই। এক ধরনের মানসিক দৌর্বল্যকে সংবাদপত্রগুলো ভাল করে বুঝত এবং তার পরিপূর্ণ সুযোগ নিয়েছিল।
এ মাথা মোটাদের কাছে ফ্রাংকফুর্টার ঝাউটুং নামক সংবাদপত্রটি সম্মানের সঙ্গে সমাদৃত হত। এরা সব সময় বেলচাকে সোজাসুজি বেলচা বলেনি। এরা সবরকম দৈহিক শক্তি প্রয়োগের বিরোধিতা করেছে এবং ক্রমাগত বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মহৎ যুদ্ধের জয়ঢাক পিটিয়ে গেছে। কিন্তু এ সংগ্রামের বিষয়টা অদ্ভুত ব্যাপার, তথাকথিত কম বুদ্ধিমানদের মধ্যে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতির এটাও একটা ভুল দিক; যা আমাদের দেশের যুবকগোষ্ঠীকে তাদের স্বাভাবিক প্রকৃতির পথ থেকে বিচ্যুত করে নিয়েছিল। সত্যিকারের জ্ঞানের বদলে কিছু এ ধরনের জ্ঞান তাদের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যার সঙ্গে সত্যিকারের জ্ঞানের কোন সামঞ্জস্য ছিল না। এ ধরনের বুদ্ধিমত্তা এবং শুভেচ্ছার শেষ প্রান্তে কিছুই মেলে না যদি সত্যিকারের লক্ষ্যবস্তু থেকে মানুষ পিছু হটে আসে। সত্যিকারের জ্ঞান তাকেই বলা যেতে পারে যা নাকি মানুষ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে অনুভব করতে সক্ষম হবে।
ব্যাপারটার আরো বিস্তারে যাই : মানুষের চিন্তাধারায় এ ভুল থাকা উচিত নয় যে সে প্রকৃতির প্রভু হওয়ার জন্যই এসেছে। শিক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োজনীয় দিকটা তাকে এ ধরনের মিথ্যা আশা দেখাতে সাহায্য করেছে। মানুষের বোঝা উচিত যে প্রয়োজনের গোড়ায় আইন-কানুনই যা নাকি প্রকৃতির রাজ্যে সর্বত্র বলবৎ তা হল যে তার অস্তিত্ব রাখার জন্য নিরবধি সংগ্রাম এবং দ্বন্দ্ব করে যেতে হবে তাকে। তখনই সে অনুভব করতে সক্ষম হবে যে মানব জাতির জন্য আলাদা কোন কানুন যে আইনের বাইরে সূর্য এবং গ্রহ-নক্ষত্র তাদের আপন কক্ষপথ পরিক্রমণ করে। চন্দ্র এবং তারকারাজি তাদের নির্দিষ্ট পথে বেয়ে চলে। সবল সর্বদাই দুর্বলের প্রভু। সুতরাং এগুলো থেকেই দেখা যাচ্ছে যাদের জন্য এসব আইন-কানুন নির্দিষ্ট, তাদের সেগুলো মেনে চলতেই হবে, অন্যথায় ধ্বংস হল অনিবার্য ফলাফল। এ চরম জ্ঞানের কাছে মানুষের উচিত নিজেকে সমর্পণ করা। সে বড়জোর তাকে বুঝতে চেষ্টা করতে পারে, কিন্তু তার নির্দিষ্ট পথ থেকে সে কিছুতেই সরে আসতে পারবে না।
আমাদের বুদ্ধিমত্তার বেশ্যাবৃত্তির জন্যই ইহুদীরা এসব সাংবাদিকতা এবং সংবাদপত্রগুলোকে বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন বলে আখ্যা দিয়ে থাকে। তাদের জন্যই ফ্রাংকফুর্টার ঝাইটুং আর বালিয়ান টাগোটে নামক সংবাদপত্রদ্বয় লিখিত। এর বক্তব্যের উদ্দেশ্যও তারাই এবং এ পত্রিকা দু’টোর প্রভাব তাদের মধ্যেই পড়েছে। অতি যত্নের সঙ্গে কর্কশ ভাষাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে; অন্যান্য শিশির থেকে বিষ বার করে এসব অনুগত জনমণ্ডলীর দেহে অতি সতর্কভাবে সেই বিষ প্রয়োগ করেছে। টগবগে স্বর এবং সুন্দর সুন্দর নির্বাচিত শব্দগুচ্ছ দ্বারা পাঠকদের জ্ঞান এবং নৈতিকতাই যে একমাত্র এসব পত্রিকার আদর্শ হওয়া উচিত সেই বিশ্বাসের পথ থেকে তাদের বিচ্যুত করা হয়েছে। অথচ বাস্তবে এসব ব্যাপারগুলো অতি ধূর্ততার সঙ্গে যে কোন বিরোধিতাকে সমূলে নষ্ট করেছে যা নাকি ইহুদী এবং তাদের সংবাদপত্রগুলোর বিরুদ্ধে যেতে পারত।
তারা পুরো ব্যাপারটাকে এমনভাবে সম্ভ্রমের সঙ্গে রূপ দিত যাতে সবাই মনে করে অন্যান্য সংবাদপত্রগুলো যে প্রশ্রয় দিত, তা যেন অত্যন্ত মৃদু বলে বোধ হয়; এবং যাতে গ্রেপ্তারী পরোয়ানাজারী করে তাদের বিরুদ্ধে কোনরকম আইনগত অধিকার প্রয়োগ না করা হয়। বাস্তবিকপক্ষে এ ধরনের কোন ব্যবস্থা সংবাদপত্রের স্বাধীন আঙিনায় অনধিকার প্রবেশেরই সমতুল্য। এ অভিব্যক্তিটা শ্রুতিকটু পদের পরিবর্তে কোমলতর বলে এ পথেই আইনের শাস্তিটাকে এড়িয়ে যেত এবং জনসাধারণকে প্রতারণা আর গণমানসকে বিষিয়ে দেওয়ার জন্যই তারা এ পথ বেছে নিয়েছিল। এভাবে শাসকবর্গ অত্যন্ত ধীরগতি সম্পন্ন হয়ে উঠেছিল; বিশেষ করে সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে আইনগত কোন ব্যবস্থা–এসব সাংবাদিক দস্যুদের বিরুদ্ধে নেওয়ার ব্যাপারে। কারণ সব সময়ই তাদের একটা ভয় যে এসব সাংবাদিক দস্যুদের বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থা নেওয়া হলে পরে জনসাধারণের সহানুভূতি যদি তথাকথিত শ্রদ্ধেয় সংবাদপত্রগুলোর ওপর গিয়ে বর্তায়! অবশ্য এ ভয় একেবারে অনর্থক ছিল তা নয়, কারণ সেই মুহূর্তে পুরো ব্যাপারটা এমন হয়ে উঠেছিল যে এ নোংরা সংবাদপত্রগুলোর মধ্যে যে কোন একটার বিরুদ্ধে কোনরকম আইনগত ব্যবস্থা নিলেই অন্যান্যরা তার সাহায্যে তৎক্ষণাৎ ছুটে আসত। এ ছুটে আসার কারণ অবশ্য এর নীতিগত সমর্থনের নিমিত্ত নয়; এর একমাত্র উদ্দেশ্য হল সংবাদপত্রের তথাকথিত স্বাধীনতা এবং জনসাধারণের মুক্ত মতামত প্রকাশের অধিকারের জন্য। এ তীক্ষ্ণ আর্তনাদ অনেক বলবান পুরুষকেই কাপুরুষে পরিণত করে; কারণ এগুলো তো নির্গত হয় তথাকথিত ভদ্রসাংবাদিক গোষ্ঠীর মুখ থেকে।
এবং এভাবেই এ বিষ জাতির জীবনের রক্তে প্রবেশ লাভ করে ও গণজীবনকে বিষাক্ত করে তোলে। সরকারের তরফ থেকে এ রোগের বিরুদ্ধে কোনরকম ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি। দ্বিমত নিয়ে যা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা সামগ্রিকভাবে পুরো ব্যাপারটাকে টেনে নিচে নামিয়েছে এবং পুরো সাম্রাজ্যটাকেই ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। যখন কোন প্রতিষ্ঠান তার কাছে যে অস্ত্র গচ্ছিত তা দিয়ে আত্মরক্ষা করতে অসমর্থ হয়, তখন তার অস্তিত্বটাই বিপন্ন হয়ে পড়ে। প্রতিটি দ্বিমত হল ভেতরকার ক্ষয়প্রাপ্ত উদাহরণ মাত্র যা সময়ে আজ অথবা কাল বাইরে বিপর্যয় ডেকে আনতে বাধ্য।
আমার দৃঢ়বিশ্বাস আমাদের বর্তমান বংশধরেরা এ বিপদের ওপরে প্রভুত্ব করতে অবশ্যই পারে যদি তাদের সঠিক পথে পরিচালনা করা যায়। কারণ এ বংশধরেরা এমন কতগুলো অভিজ্ঞতার রাস্তা অতিক্রম করেছে যা তাদের স্নায়ুকে শক্ত করে তুলতে সক্ষম।
আমার দৃঢ় অভিমত হল এ কাজ পূর্ব পুরুষদের চেয়ে আমাদের পক্ষে করা অনেক সহজ। বারো ইঞ্চি একটা অস্ত্রের ভেদ ক্ষমতা হাজার ইহুদী সংবাদপত্রের সর্প-শব্দের চেয়ে অনেক বেশি তীব্র।
জার্মানিতে প্রধান এ সমস্যাগুলোকে কী ধরনের দুর্বল এবং সন্দেহপূর্ণ চিত্তে সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল : পরস্পর হাতে হাত দিয়ে রাজনৈতিক এবং নৈতিক জীবনকে বিষাক্ত করে তোলা। বহু বছর ধরে এ তুলনামূলক বিষাক্ত পদ্ধতি গণমানসকে অসুস্থ করে তুলেছে। বড় শহরে বিশেষ করে ছড়িয়ে পড়েছে সিফিলিসের মত ভয়ঙ্কর রোগ; দেশের সর্বপ্রান্তে রাজরোগ ধীরে ধীরে পা রেখে জীবনকে কেড়ে নিচ্ছে। অর্থাৎ তার নির্দিষ্ট ফসল সে নিশ্চিন্তে ঘরে তুলে চলেছে।
যদিও এ দুই ক্ষেত্রেই জাতির জীবনে বিপদের সংকেত জানিয়ে চলেছে; পুরো ব্যাপারটা দেখে শুনে মনে হয় যে কেউই এ প্রতারণার ব্যাপারে কোনরকম সক্রিয় ব্যবস্থা নেয়নি। বিশেষ করে সিফিলিসের ব্যাপারে তো মনে হয় সমগ্র রাষ্ট্র এবং গণমানস পুরোপুরি এর কাছে আত্মসমর্পণ করে বসে আছে।
এ পরিস্থিতির বিরোধিতার মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন ছিল সত্যিকারের যতটুকু পরিষ্কার করা হয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি জোরের সঙ্গে সমস্ত ব্যাপারটাকে ঝাড় দিয়ে পরিষ্কার করার। এখানেও একমাত্র রোগকেই সোজাসুজি আক্রমণ করা শ্রেয়, রোগের উপসর্গগুলোকে নয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও প্রধান কারণটা এভাবে নির্ণীত হওয়া উচিত যাতে ভালবাসাটাকে বেশ্যাবৃত্তির নামান্তর বলেই প্রতিভাত হয়। যদিও এ পথে ভয়ানক এ ব্যাধিকে আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়, জাতিকে আরো অনেক বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে। কারণ এ বেশ্যাবৃত্তির থেকে যে নৈতিক অধঃপতরেন সৃষ্টি তা জাতিকে আরো বেশি নিচে টেনে নামাবে। ধীরে হলেও নিশ্চিতরূপে। আমাদের আধ্যাত্মিকতাবাদকে ইহুদীকরণ এবং আমাদের সহজাত প্রবৃত্তিকে ধনলোভী করে তোলার ফলাফল আজ হোক কাল হোক আমাদের ভাবীকালের ওপর তা’ আঘাত হানতে বাধ্য। দৃঢ় এবং স্বাস্থ্যবান সন্তান, যারা প্রকৃতির আশীর্বাদধন্য, তাদের পরিবর্তে আমাদের ঘর-সংসার ভরবে এমন কতগুলো সন্তানে যারা এ অর্থনৈতিক হিসেবের ফলশ্রুতি হিসেবে মানবজাতির নমুনাস্বরূপ হবে। অর্থনৈতিক কারণও দিনের পর দিন বিবাহের ভিত্তি হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভবিষ্যতে বিবাহের এটাই একমাত্র কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ভালবাসা তখন তার বহিঃপ্রকাশের জন্য অন্য পথ খুঁজে নেবে।
এখানেও অন্যান্য ক্ষেত্রের মত প্রকৃতিকে কিছু সময়ের জন্য অস্বীকার করা যেতে পারে। কিন্তু আজ হোক কাল হো সে তার নির্মম প্রতিশোধ নিয়ে ছাড়বে। এবং মানুষ যখনই এ সত্য উপলব্ধি করবে, তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।
আমাদের নিজস্ব উদারতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ যে প্রাথমিক বিবাহবন্ধনের কারণগুলোকে আমরা কিভাবে লুণ্ঠন করেছি ক্রমাগত সেইগুলোকে অস্বীকার করে। এখানেও মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে সেই আমাদের চিরাচরিত অভ্যাস; একদিকে সামাজিক সমস্যার চাপ, অপরদিকে অর্থনৈতিক অবস্থা। একটা আমাদের নিয়ে গেছে বংশগত দুর্বলতার পথে, আরেকটা মিশ্রিত রক্তে। বড় বড় দোকানের ইহুদী মালিকদের কন্যারা মহাপ্রভুদের বংশবৃদ্ধির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সঙ্গিনী বলে বিবেচিত এবং এ সঙ্গিনীদের সম্পর্কে সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি সত্যই অত্যন্ত প্রখর। এ সমস্তই সমাজকে অধঃপাতে নিয়ে চলেছে। বর্তমানে আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজও সেই পথেই এগিয়ে চলেছে। তাদের যাত্রাপথের শেষে বিন্দুর লক্ষ্যও সেই একই বিন্দুতে।
এ অস্বস্তিকর সত্যটাকে তড়িঘড়ি এবং উত্তেজনাহীন অবস্থায় মার্জনা করে সরিয়ে একপাশে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এমনভাবে পুরো ব্যাপারটাকে রূপ দেওয়া হয়েছে যে এভাবে সমস্ত ব্যাপারটাকেই মুছে ফেলা সম্ভব।
কিন্তু না এটাকে অস্বীকার করার উপায় নেই যে আমাদের শহর এবং নগরগুলোর লোকসংখ্যার বিরাট একটা অংশ বেশ্যাবৃত্তিতে আসক্ত হয়ে পড়েছে; কারণ হল প্রণয়ের প্রতি তাদের সহজাত প্রবৃত্তি। এবং তাদের নিজেদের জীবন বিভিন্ন যৌনব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে কলুষিত হয়ে চলেছে। ঘরের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যেই তা স্পষ্ট প্রতিভাত। এগুলো হল দুঃখজনক এবং বিষাদময় ঘটনার সাক্ষ্য যে আমাদের যৌনজীবনে কষাঘাত কত তীব্র হয়ে উঠছে। এ যন্ত্রণায় প্রত্যক্ষ ফলাফল হল পিতামাতার পাপ।
এ অস্তিত্বময় এবং চরম সত্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার অনেক পথ আছে। বহু লোকই অন্ধভাবে জীবনের পথ চলে। অথবা চোখ খোলা রাখলেও চারপাশের অনেক কিছু দেখতে চায় না। কিছু লোক আবার নিজস্ব মতবাদের জালে নিজেদের আবদ্ধ রাখে। এটাই হল জীবনের কদর্যময় দিকগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার সস্তা এবং সোজা পথ। পুরো ব্যাপারটাই যেন মিথ্যা এবং হাসির ঘটনা। যখন পুরো ব্যাপারটা এর মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়, তারা সমস্ত ব্যাপারটাকে পাপ-পূর্ণ এবং জীবিকাবিহীন বলে। আক্ষেপ করে।
শেষে যারা এ চাবুকের দ্বারা কি ভয়ঙ্কর ফলাফল হবে বুঝতে পেরেছিল তারাও শুধু কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে তাদের দায়-দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলেছে; কারণ তারা বুঝেছে এ ধ্বংসের সামনে তারা সম্পূর্ণ অসহায়। সুতরাং পুরো ব্যাপারটাই তার আপন গতি পথে এগিয়ে চলে।
সন্দেহ নেই সমস্ত ব্যাপারটাই সুবিধেজনক এবং সহজ; শুধু এর সুবিধাজনক দিকটাই আমাদের জাতীয় জীবনে চরম বিপদ ডেকে এনেছে। অন্যান্য জাতিরা আমাদের থেকে উন্নত নয়, এর দোহাই দিয়ে আমাদের জাতির অধঃপতন কোনরকমেই ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। শুধু যন্ত্রণাটার ওপর সহানুভূতির প্রলেপ মাখিয়ে সহ্য করার পথটাকে সুগম করে তোলা যায় মাত্র। কিন্তু প্রয়োজনীয় যে প্রশ্নটা এখানে থেকে যায় : কোন্ জাতি এ চাবুকের কষাঘাতের আঘাত প্রথমে এড়িয়ে উঠবে, এবং কোন জাতি এর বশ্যতা স্বীকার করবে। সেটাই হবে জাতির পক্ষে সমস্ত পরিস্থিতির চূড়ান্ত পরিণাম। বর্তমানে জাতির মূল্যায়নের পরীক্ষার সময় চলেছে। যে জাতি এ পরীক্ষায় পাশ করতে অক্ষম, তাদের মৃত্যু অনিবার্য এবং তাদের জায়গা তাদের চেয়ে অধিকতর বলবান এবং স্বাস্থ্য সম্পন্ন জাতি দখল করবে; যারা আরো বেশি দুঃখ কষ্ট সহ্য করে নিতে সক্ষম। যেহেতু বিশেষ করে এ সমস্যা ভাবীকালের, সেইহেতু যে কোন পিতা মাতার পাপ তার বংশের দশম পুরুষেও গিয়ে পর্যন্ত বর্তায়। রক্ত এবং জাতির পবিত্রতা লঙ্ন করার ফলাফল এ চরম দুর্দশা।
এ রক্ত এবং জাতির বিরুদ্ধে পাপ হল এ পৃথিবীতে বংশানুক্রমে এবং যে জাতি এ পাপে পাপী তার ধ্বংস অনিবার্য।
যুদ্ধ পূর্ব–জার্মানিতে এ প্রধানতম সমস্যাটার প্রতি যে দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছিল তা’ রীতিমত লজ্জাজনক। আমাদের যুবকদের একটা বিরাট অংশ যাদের বড় বড় শহরে বাস, তাদের ভেতরে এ জীবাণুর অনুপ্রবেশ বন্ধ করার কি কোনরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল? অথবা, আমাদের যৌনজীবনকে কলুষিত এবং ধ্বংস করার বিরুদ্ধেই বা কি করা হয়েছিল? অথবা, আমাদের সমর্থ জাতীয় জীবনে এবং সিফিলিস রোগ ছড়িয়ে পড়ার বিরুদ্ধেই বা কতটুকু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল? এর সবচেয়ে ভাল উত্তর হল কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ছিল?
এলোমেলো পথে এ সমস্যার মোকাবিলা করার চেয়ে শাসকবর্গের চিন্তা করা উচিত ছিল যে এ সমাধানের ওপরেই ভবিষ্যত বংশাবলীর কল্যাণ নিহিত। তবে এটাও স্বীকার করে নেওয়া উচিত যে এ সমস্যার মোকাবিলা একমাত্র নির্মম পথেই করা চলে। প্রাথমিক কাজ হল সমস্ত জাতির একাগ্রতা এ বিপদের দিকে নিবদ্ধ করা উচিত; যাতে প্রত্যেকটি ব্যক্তি এর বিরুদ্ধে সন্ত্রামের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে। ব্যক্তিগত কোন চরিত্রের ওপর বাধা নিষেধ আরোপ করাটাও অনর্থক, বা তার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না পুরো ব্যাপারটাকে জনসাধারণ মেনে নিচ্ছে। সর্বব্যাপী এবং শৃখলাবদ্ধভাবে এ সমস্যার এমন মোকাবিলা করতে হবে যাতে সমস্ত গণমানসের নজর এদিকেই পড়ে। এবং অন্যান্য দৈনিক সমস্যাগুলোকে কিছু সময়ের জন্য সরিয়ে পিছু হটিয়ে দেয়।
প্রতিটি ক্ষেত্রে যেখানে দেখা যাবে যে গণমত তৈরির ব্যাপারে সমস্যাটা যথেষ্ট পরিমাণে জটিল, সেখানে উচিত একটা সমস্যার প্রতি মনোনিবেশ করা; সে মনোযোগ এমন হওয়া উচিত যে যাতে এটা জীবন মরণ সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হয়। একমাত্র এ পথেই গণমানসকে এমন একটা উঁচু ধাপে জাগরিত করা সম্ভব যে জনতার অদম্য ইচ্ছার সঙ্গে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রচেষ্টা মিলিত হয়ে ফলাফল যথেষ্ট পরিমাণে উন্নতি ঘটাবে।
ব্যক্তিগত জীবনেও এ সত্য কার্যকরী, অবশ্য যদি সে জীবনে মহান কিছু অর্জন করতে সচেষ্ট হয়। সে তার অগ্রগতির নির্দিষ্ট একটা ধাপে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখবে এবং সেই ধাপ পার হওয়ার পরেই একমাত্র পরের ধাপে আরোহণের চেষ্টা করবে। যারা তাদের উদ্যম ধাপে ধাপে ওঠার চেষ্টায় ব্যয়িত করে না, এবং সমস্ত শক্তি প্রতিটি ধাপ অতিক্রমের নিমিত্ত ব্যয়িত হয় না তাদের পক্ষে শেষ এবং কাম্য বস্তু অর্জন করা সম্ভব নয়।
সুতরাং ওপরের বক্তব্য অনুসারে দেখা যাচ্ছে মানবজীবনের রাস্তাটা অতিক্রম করতে হলে জনতাকে বোঝানো উচিত যে তাদের সংগ্রামের পরবর্তী বস্তু হল মাত্র একটাই; এবং তার ওপরেই পরের ধাপে সমস্ত কিছু নির্ভরশীল। জনতার পক্ষে তাদের সামনের বিস্তীর্ণ রাস্তাটা নজরে আনা কিছুতেই সম্ভব নয়। যাতে তারা সেই বিস্তীর্ণ রাস্তা অতিক্রম করতে গিয়ে ক্লান্ত এবং অবসন্ন না হয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের লব্ধ বস্তু মনে রাখতে সক্ষম; কিন্তু ছোট ছোট ধাপ ছাড়া পুরো রাস্তা অতিক্রম করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়; যেমন পথিক জানে তার পথের শেষ কোথায়! কিন্তু অনাদি পথ তো চিন্তার জগতের বাইরে। একমাত্র এভাবে আমরা তার লক্ষ্য বস্তুতে পৌঁছানো পর্যন্ত সেটার উদ্যম বজায় রাখতে পারি।
এ পথে সমস্ত প্রচারকার্যকে কেন্দ্রীভূত করেই যৌনরোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তাটাকে আমরা জনসাধারণের সামনে তুলে ধরতে পারি। এবং এটাকে এমনভাবে করতে হবে যে জাতির জন্য এটা একটা কাজ বলে নয়; জাতির পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ, বর্তমানে এ মনোভাব জনতার মধ্যে তৈরি করে। গণমানসের কাছে এ সত্যতাকে স্পষ্টরূপে তুলে ধরার জন্য সমস্ত রকমের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্রীভূত করার প্রয়োজন, যতক্ষণ না পর্যন্ত সমস্ত জাতি চিন্তা করে যে এ সমস্যার সমাধানের ওপরেই সমগ্র জাতির ভবিষ্যত নির্ভর করছে; এককথায় বলা যেতে পারে উজ্জ্বল ভবিষ্যত অথবা জাতির অবলুপ্তি।
একমাত্র এ প্রাথমিক আয়োজনের পর–প্রয়োজনে এ সময়ের ব্যাপ্তি কয়েকমাসও হতে পারে, গণমানস এবং সংকল্পকে পরিপূর্ণরূপে জাগরিত করা সম্ভব। একমাত্র তখনই গভীর এবং নির্দিষ্ট একটা পন্থা নেওয়া যাবে, কারণ তখন তো গণমানস সমস্যার মুখোমুখি হওয়ার জন্য সম্পূর্ণভাবে তৈরি; তাই জনসাধারণের ইচ্ছাশক্তির ঘাটতি তাতে থাকবে না। স্পষ্ট মনে রাখা উচিত এসব আবর্জনা ঝেটিয়ে সরানোর জন্য প্রয়োজন প্রচুর আত্মত্যাগ এবং প্রচণ্ড রকমের পরিশ্রমের। যৌনরোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অর্থ হল বেশ্যাবৃত্তি, ভুয়া সংস্কার, মিথ্যা জনমত ইত্যাদির বিরুদ্ধে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর ভেতরে সংগ্রাম বিশেষ।
রাষ্ট্রের এ সংগ্রামে নামার আগে প্রথমেই দেখে নিতে হবে যুবক সম্প্রদায় যেন ছোট বয়সে বিয়ে-সাদীর সুযোগ পায়; বেশি বয়সের বিয়ের আমরা যত যুক্তিই দেখাই না কেন, মানবজাতির কাছে ব্যাপারটা লজ্জাকর।
বেশ্যাবৃত্তি মনুষ্যত্বের পক্ষে কলঙ্কবিশেষ। এবং এ বৃত্তি দয়াদাক্ষিণ্য বা শিক্ষা দ্বারা দূর করাও সম্ভব নয়। এর সীমাবদ্ধতা এবং দূরীকরণ একমাত্র সম্ভব, যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে এ বৃত্তিকে মুক্ত করা যায়। তার জন্য প্রয়োজন যুবক যুবতীদের অল্প বয়সে বিবাহের সুযোগ দান। এটাই হল এ বৃত্তি দূরীকরণের প্রধান উপায়।
এসব কারণে মানুষ এত সহজে বিপথগামী হয় যে ইদানীং যে কোন মাকে বলতে শোনা যাবে যে তার মেয়ের জন্য সে ভাল ছেলে খুঁজে পাচ্ছে না। আর সে কারণে বেশ্যাদের প্রতি আসক্ত কোন ছেলেকেই বাধ্য হয়ে সে মেয়ে বিয়ে করে। এ সঙ্গী নির্বাচনের ফলে তাদের সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যত যা হওয়া উচিত, তাই হয়ে থাকে।
একটু চিন্তা-ভাবনা করলেই যে কেউ উপলব্ধি করতে পারবে যে পুরো পদ্ধতিটাই সার্থক বংশাবলী উৎপাদনের বিরোধী। এবং প্রকৃতিতে জেনে শুনে তার অধিকার থেকে প্রতারণা করা হচ্ছে; তা হলে একটা প্রশ্নই থেকে যায় : বিবাহ বলে ব্যাপারটার অস্তিত্ব এখনো রয়েছে কেন? এবং তার কাজটাই বা কী? এটাত তা হলে বেশ্যাবৃত্তির নামান্তর। আমাদের উত্তর পুরুষদের জন্য তবে কি আমাদের কোন মাথা ব্যাথাই নেই? অথবা লোকে বুঝতে পারছে না যে প্রকৃতি তার অভিশাপ ধীরে ধীরে তাদের ওপরে আরোপ করছে এবং ভবিষ্যত বংশাবলীকে তাদের এ নির্বুদ্ধিতার জন্য প্রকৃতির এক ভীষণ নিষ্ঠুর আইন কানুনের মুখোমুখি হতে হবে? এভাবেই তথাকথিত সভ্য জাতিরা অধঃপতনে যায় এবং একসময় ধ্বংস হয়।
বিবাহেই বিবাহের সমাপ্তি নয়; এর আরো মহৎ উদ্দেশ্য আছে। যার প্রধান কাজ হল উৎকৃষ্ট মানবজাতি তৈরি করা এবং সেই মানকে ধরে রেখে বাড়িয়ে চলা। এটাই হল বিবাহের সত্যিকারের অর্থ এবং উদ্দেশ্য।
এ অর্থ এবং উদ্দেশ্যকে যদি মেনে নেওয়া হয়, তবু লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য যে পথের প্রয়োজন, তাকেও মেনে নিতে হবে। সুতরাং অল্প বয়সে বিবাহটাকে আইন করে দেওয়া উচিত। কারণ অল্পবয়সী যুবক-যুবতীদের মধ্যে এখনো সেই আদিম শক্তি বর্তমান যা নাকি সফল উত্তর পুরুষ উৎপাদনের ব্যাপারে গর্বের বস্তু এবং যে শক্তি বর্তমানেও অব্যাহত। অবশ্য বাল্যবিবাহ আইন করে করা সম্ভব নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না তার জন্য যেসব ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন, সেগুলো মেটানো সম্ভব হচ্ছে। এমন কি তার আগে ব্যাপারটা চিন্তা করাই উচিত নয়। অন্য ভাষায় বলতে গেলে এ সমস্যার সমাধান যদিও আপাতদৃষ্টিতে সমস্যাটাকে সহজ সরল সামাজিক পটভূমিকার মৌলিক পরিবর্তন ছাড়া কখনই সম্ভব না। এবং এ সমস্যার মোকাবিলা করার ব্যবস্থাটাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখে তবে প্রয়োগ করা উচিত। বিশেষ করে তথাকথিত গণতন্ত্র যখন বাড়ি ঘরের সমস্যাটাকে এখনো সমাধান করতে পারেনি।
আমাদের অর্থহীনের মত বেতন ব্যবস্থাও বাল্যবিবাহের বিরোধী, যার দ্বারা নাকি পরিবার প্রতিপালন একেবারেই অসম্ভব। অতঃপর দেখা যাচ্ছে বেশ্যাবৃত্তিকে যথার্থ উপায়ে মোকাবিলা করার জন্য মৌলিক সামাজিক পরিবর্তনের একান্ত প্রয়োজন এবং তারপরেই বাল্যবিবাহ চালু করা সহজ হয়ে দাঁড়াবে। এ সমস্যার সমাধানের এটা হল প্রাথমিক নিয়ম।
দ্বিতীয়ত, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি এবং সন্তান প্রতিপালনের মূল প্রথাগুলোর অবিলম্বে মূলোৎপাটন করা-যে কারণগুলোয় কাউকেই সবিশেষ চিন্তিত দেখা যায় না। আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে ভারসাম্য আনার প্রয়োজন, বিশেষ করে মানসিক এবং দৈহিক ব্যাপারে।
আমাদের মাধ্যমিক স্কুল বলে যা আজ পরিচিত, তা গ্রীক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি অপমান ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি এটা ভুলে গেছে যে একমাত্র সুগঠিত শরীরেই চরিত্রবান মানুষ পাওয়া যেতে পারে। এ বক্তব্য কিছুটা হেরফের করে সমগ্র জনতার পক্ষে উপযোগী করা যায়।
যুদ্ধ পূর্ব জার্মানিতে সময়টা এমন ছিল যখন কেউ সত্যের ওপরে কিছু চিন্তা-ভাবনা করতে চাইত না। শরীরচর্চাকে প্রচণ্ড রকমের অবহেলা করা হত; জাতির উন্নতির পক্ষে মনের একদিককার অনুশীলনকেই যথেষ্ট বলে বিবেচিত হত। এ ভুলের প্রতিক্রিয়া নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই দেখা দেয়। বলশেভিক শিক্ষা যে এসব রাজ্যগুলোতে বিস্তৃতি লাভ করে, তা’ কোন হঠাৎ ঘটনার ফলশ্রুতি নয়। কারণ সেইসব প্রদেশের অধঃপতিত লোকগুলো উপবাসের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ মধ্য জার্মানি, স্যাস্কনি এবং রুড় উপত্যাকার কথা বলা চলে। এসব জেলাগুলোতে কোনরকম বাধা বলতে যা বোঝায় তা এরা পায়নি। এমন কি ইহুদী-রূপ রোগ সংক্রমণের বিরুদ্ধে সমাজের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় থেকেও কোনরকম বাধা আসেনি। এর সহজ কারণ হল বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় নিজেরাই শারীরিক দিক থেকে তখন অধঃপাতে গেছে; কষ্ট বা ক্লেশের দরুণ এ অধঃপতন নয়। নিছকই শিক্ষাপদ্ধতির ফল। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকটা যা আমাদের সমাজের উঁচু শ্ৰেণীর মধ্যে প্রচলিত, বর্তমান যুগের জীবন সংগ্রামের জন্য তা সম্পূর্ণরূপে অনুপযোগী। সুতরাং তারা তাদের নিজেদের প্রতিপালনে অক্ষম। জীবনধারণের ক্ষেত্রেও তাদের সক্ষমতা কোথায়। প্রায় প্রতিটি কাপুরুষতার ক্ষেত্রে দৈহিক অপুষ্টি হল আসল কারণ।
অবিবেচনা ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিজীবী শিক্ষা-ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। তার ফলাফল হল দৈহিক শিক্ষার অবনতি; যার পরিণতি হল অল্প বয়সের যৌন চিন্তায়। যেসব ছেলেদের খেলাধূলার মাধ্যমে শরীর গঠন হয়, তাদের যৌন প্রবণতা অন্যান্য ছেলেরা যারা শুধু ঘরে বসে মনের খোরাক জুগিয়ে চলেছে, তাদের চেয়ে অনেক কম। সত্যিকারের শিক্ষাপদ্ধতি জীবনের এ দিকটাকে অবহেলা করতে পারে না। এবং আমাদের স্মরণে রাখা উচিত যে স্বাস্থ্যবান পুরুষ এবং স্বাস্থ্যবতী মহিলা কোন দুর্বল প্রাণীর জন্ম দেবে না। যারা জন্মের পরেই দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে।
এভাবে আমাদের শিক্ষার সমস্ত শাখাকে ছকে বাধতে হবে যাতে ছেলেরা তাদের অবসর সময়টাকে শরীর চর্চার কাজে লাগাতে পারে। সে বছরগুলো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে কাটিয়ে যেন তার শরীর গঠন করতে পারে। সিনেমা দেখে নষ্ট করার কোন অধিকার তার নেই। কিন্তু যখন তার দিনের কাজ সাঙ্গ হবে, সে যেন তার শরীর গঠন করতে পারে। কারণ প্রয়োজনের সময় যেন তার শরীর গঠনের ব্যাপারে ঘাটতি না পড়ে। আমাদের শিক্ষা পদ্ধতির এটাও একটা বড় দায়িত্ব, তবু জ্ঞান বা বিজ্ঞতাই তার ভেতরে জোর করে ঢুকিয়ে দেওয়া নয়। আমাদের স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে প্রতিটি ছাত্রের মনে দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায় যে শরীর তৈরি করার দায়িত্ব তার নিজের ওপরে অর্পিত। উত্তর পুরুষের কাছে পাপ রূপে গণ্য হয় এমন কিছু বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা তাদের নেই, কারণ তাহলে সেটা জাতির বিরুদ্ধেই কাজ করা হবে।
মনের অসুস্থতার সঙ্গে সংগ্রামের জন্য শরীর গঠনের বিশেষ প্রয়োজন। আজকের গণজীবন যেন যৌন উত্তেজনার বিরাট একটা চুল্লী। চলচ্চিত্র, নাটক এবং খেলাধূলা করার জায়গাগুলোর দিকে একনজর ফেললেই বোঝা যায় যে এগুলো আমাদের সঠিক পরিবেশ নয়। বিশেষ করে আমাদের যুবকদের পক্ষে। বিজ্ঞাপনপত্র এবং বিজ্ঞাপনের জন্য টাঙানো বিজ্ঞপ্তিগুলো জনতাকে অত্যন্ত ইতরভাবে আকর্ষণ করে। যে এখনো তার যৌবনোথ প্রবল ইচ্ছা হারায়নি, তাদের স্পষ্ট বুঝতে এতটুকু কষ্ট হবে না যে এগুলোর পরিণতি কি ভয়ানক। এ কাম যা নাকি খারাপ কাজে প্ররোচনামুলক, যুবকদের মাথায় ঘোরে। তারা বুঝতেই পারে না ব্যাপারটা কি। দুর্ভাগ্যবশত এ শিক্ষাব্যবস্থার ফলাফল কি তা আমাদের সমকালীন যুবকদের দেখলেই বুঝতে পারা যাবে। যারা অকালে পরিণত হয়, তারা সহজেই জুড়িয়েও যায়। মাঝে মাঝে আমাদের চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়স্ক ছেলেদের ওপর আইন তার আলো ফেলে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে এ বয়সের ছেলেরাও যৌন রোগগ্রস্ত। এটা কি দুঃখ এবং লজ্জাজনক নয় যে অসংখ্য দৈহিক দুর্বল এবং বুদ্ধির দিক থেকে নষ্ট যুবক ছেলেরা যারা বিয়ের নামে বড় শহরে গণিকাদের সঙ্গে বসবাস করছে।
যারা সত্যিকারের গণিকাবৃত্তির বিরুদ্ধে সততার সঙ্গে সংগ্রাম করতে ইচ্ছুক, তাদের প্রথমেই যে কারণে গণিকাবৃত্তি প্রসারলাভ করেছে সেই কারণগুলোকে দূর করতে হবে। নির্ভর চিত্তে তাদের দূষিত নীতিগুলোকে সরাতে হবে যা নাকি আমাদের কালচারকে বিষাক্ত করে তুলেছে। এবং তার জন্য যে আর্তনাদই উঠুক না কেন, তাতে ভয় পেলে চলবে না। আমরা যদি আমাদের যুব সমাজকে আজকের এ পঙ্কিল পরিবেশ থেকে টেনে নিয়ে না আসি, তা হলে এ পঙ্কিল পরিবেশ তাদের গ্রাস করে ফেলবে। যে সব নেকি এসব দেখতে চায় না, তারা কিন্তু অপ্রত্যক্ষভাবে এ পরিবেশকে বাড়াতেই সাহায্য করে চলেছে। এবং ভবিষ্যতের আঙিনায় এ গণিকাবৃত্তি ছড়িয়ে পড়ার জন্যও তারা দায়ী। শুধু এ নয় যে তারা উত্তর-পুরুষদের কাছে এর জন্য কি জবাব দেবে! আমাদের কালচারের এ বিশুদ্ধিকরণের প্রয়োজনীয়তা জীবনের সর্বক্ষেত্রে। অভিনয়, শিল্পকলা, সাহিত্য, চলচ্চিত্র, সংবাদপত্র, বিজ্ঞাপন ইত্যাদিতে এ ছোপ লেগে রয়েছে, তার থেকে এ ছোপ মুছে ফেলে জাতির উদ্দেশ্যে তা’ উৎসর্গ করতে হবে। জনসাধারণের জীবন তথাকথিত আধুনিক প্রেম সম্বন্ধীয় ব্যাপার-স্যাপারগুলো থেকে মুক্ত করতে হবে; শুধু তাই নয় পৌরষত্যহীন এবং অতি বিনয়ী ভাবধারাগুলো থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করা উচিত। এসব করতে গিয়ে আমাদের নজর রাখা উচিত যে পদ্ধতি নেওয়া হবে তা যেন অত্যন্ত চিন্তার সঙ্গে বিবেচনা করা হয়, যাতে শরীর এবং মনকে জাতির মঙ্গলের জন্য উন্নত করা যায়। একটা জাতির রক্ষার ব্যাপারে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দ্বিতীয় পর্যায়ের বিবেচনা।
এসব ব্যবস্থা নেওয়ার পরেই একমাত্র এ অভিশপ্ত চাবুকের বিরুদ্ধে ভেষজবিদ্যা প্রয়োগের প্রচার করা উচিত এবং তাতে কিছুটা হলেও সাফল্য লাভ করা সম্ভব। কিন্তু এখানে আবার দোমনা ভাব কিন্তু অর্থহীন। দূরদর্শিতা এবং প্রয়োজনীয় পদ্ধতিকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। দ্বিধাগ্রস্ত মন নিয়ে এগোলে অসুস্থ এক জনের বীজ সুস্থ শরীরে ছড়িয়ে পড়ে সেই অসুস্থতা ক্রমাগত বেড়েই চলবে। এটা শেষ পর্যন্ত হয়ে দাঁড়াবে এক ধরনের মনুষ্যত্ব যা নাকি একজনকে বাঁচাতে গিয়ে হাজার জনের ধ্বংস অনিবার্য। অপরিপূর্ণ লোকদের ধারা পঙ্গু বংশ বাড়িয়ে চলার দাবিকে উপেক্ষা করা যে কোন জাতির পক্ষে খুবই অসম্ভব ব্যাপার, যার ভিত যথেষ্ট শক্ত মাটিতে প্রোথিত। হাজার হাজার মানুষের ক্ষেত্রে অসুখী এবং দুঃখ যন্ত্রণাটাকে কাটিয়ে ওঠা এ পদ্ধতিকে কাজে লাগালে সম্ভব হবে। এতে জাতির স্বাস্থ্য ধীরে ধীরে উন্নতি লাভ করবে। সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করে গেলে তা যৌন রোধ বিস্তারের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। বর্তমান শতাব্দীর সাময়িক বেদনা হাজার হাজার বছরের যন্ত্রণার থেকে আমাদের দেশের মানুষকে মুক্তি দেবে।
সিফিলিস্ এবং এর পটভূমি গণিকাবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম সমগ্র মানবজাতির পক্ষে বিরাট একটা কাজ।
কিন্তু আলস্য এবং কাপুরুষতার জন্য যদি এ যুদ্ধ খতম করার সগ্রামে প্রকৃত মানুষ হয়; তবে আমাদের কল্পনা করে নিতে বোধকরি কষ্ট হবে না যে পাঁচশো বছর পরে এর ফলাফল কি হয়ে দাঁড়াবে। ঈশ্বরের ছায়া মানুষের চরিত্রে অতি কম পরিমাণেই অবশিষ্ট থাকবে; একমাত্র দৃষ্টিকর্তাকে ব্যঙ্গ বা উপহাস করা ছাড়া।
তবে জার্মানিতে এ কশাঘাতের প্রতিশোধক হিসেবে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? যদি আমরা এর উত্তরের জন্য শান্তভাবে চিন্তা করি, তা আমাদের হতাশই করবে। এটা সত্যি যে সরকার যদি এ রোগের ভয়ানক প্রকৃতি এবং ক্ষতিজনক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে অবহিত ছিল। তবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা সম্বন্ধে যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, তা শুধু নিরর্থকই নয়, অনর্থকারীও বটে। তারা রোগের কারণটা সম্পর্কে উদাসীন থেকে নিরাময়ের লক্ষণগুলো বেছে নিয়ে সে রোগ সাময়িক চাপা দেবার ব্যবস্থা করত। বেশ্যাদের ডাক্তারী পরীক্ষা করা হত এবং যতটা সম্ভব আয়ত্তে রাখার চেষ্টা হত; তবু রোগের লক্ষণগুলো যখন সর্বাঙ্গে ফুটে বের হত, তখন তাদের পাঠানো হত হাসপাতালে। চিৎকার আর্তনাদ জুড়ে দিলে মনুষ্যত্বের কারণে তাদের আবার ছেড়েও দেওয়া হত।
এটাও সত্যি যে সংরক্ষণ আইন যা পাশ করা হয়েছিল তাতে সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়ে যৌন সহবাস করাটা রীতিমত শাস্তিমূলক। অথবা যারা যৌন কোন রোগে ভুগছে। তাদেরও শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে যদি সহবাস করে। তত্ত্বের দিক থেকে ঠিকই ছিল; কিন্তু বাস্তবে সম্পূর্ণ রূপে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মেয়েরা পুরুষদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্য আদালতে উপস্থিত হত না যারা তাদের স্বাস্থ্য এবং ভবিষ্যত হরণ করেছে। কারণ এসব ক্ষেত্রে পুরুষদের থেকে মেয়েদের বেলায় অনেক বেশি অশিষ্ট মন্তব্যের আশঙ্কা। এবং যে কারোর পক্ষে সহজেই এটা অনুমেয় তাদের অবস্থা কি হয়ে দাঁড়াবে যদি তাদের মধ্যে এ রোগ স্বামীদের দ্বারা ছড়িয়ে থাকে। মেয়েরা কি এ ক্ষেত্রেও তাদের নালিশ নিয়ে এগিয়ে আসবে? অথবা তারা কি করবে?
ছেলেদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটাতে আরেকটা সত্য নিহিত, বিশেষ করে তারা যখন মাদক দ্রব্যের নেশায় থাকে তখন তাদের অজ্ঞাতসারেই এ বিপদের দিকে ছুটে চলে। তার অবস্থাই তাকে প্রণয়ের সত্যিকারের সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে দেয় না। প্রতিটি রোগ এস্ত গণিকা পুরুষের এ অবস্থায় সুযোগের জন্য প্রতীক্ষা করে। এর ফলাফল হল এ যে হতভাগ্য পুরুষ পরে তার এ অবস্থার সত্যিকারের হিতকারী পৃষ্ঠপোষক যে কে তা আর স্মরণে আনতে পারে না। এটা বার্লিন বা মিউনিকের মত বড় শহরে কোন আশ্চর্যজনক ঘটনাই নয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গাঁয়ের থেকে শহরে আসা লোক ব্যাপার-স্যাপার দেখে এত নির্বাক ও বশীভূত হয়ে পড়ে যে গণিকারা সহজেই তাদের লুণ্ঠন করে।
সবশেষে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে (কে বলতে পারে যে) রোগের সংক্রমণ তার মধ্যে হয়েছে কিনা? অসংখ্য ক্ষেত্রে দেখা গেছে ওপর ওপর দেখতে নিরোগ লোকেরও পরে রোগটা আবার উদয় হয়েছে এবং তার অজ্ঞাতেই তাকে কুড়ে কুড়ে খেয়ে চলেছে।
সুতরাং বাস্তব ক্ষেত্রে এ সংরক্ষণ আইনের ফলাফল নেহাত-ই নেতিবাচক। গণিকাবৃত্তির ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই। শেষমেষ চিকিৎসা ও নিরাময়ের ব্যাপারেও ব্যাপারটা খুব নির্ভরযোগ্য ও সন্দেহাতীত নয়। খালি একটা জিনিস দিনের আলোর মত স্পষ্ট; তা; হল এ কশাঘাত দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। যে ব্যবস্থাই নেওয়া হয়ে থাক না কেন, এ ব্যাপারটা তাদেরই অপদার্থতা প্রমাণ করার পক্ষে যথেষ্ট।
বাকি ব্যাপারগুলোও একই ব্যাপারের মত নিরর্থক। মানুষের গণিকাবৃত্তি কমা দূরে থাক, কোন কিছুই ফললাভ হয়নি।
যারা এ ব্যাপারের সঙ্গে একমত নয়, তাদের কাছে বিনীত অনুরোধ তারা যেন এ রোগের সংখ্যাতত্ত্বের দিকটা দেখে, গত শতাব্দীতে এর বৃদ্ধি এবং সমকালীন অবস্থায় এর বৃদ্ধির সম্ভাবনা কি রকম। সাধারণ পর্যবেক্ষক-যদি সে একেবারে নির্বোধ না হয়, তবে পুরো ব্যাপারটা তার কাছে পরিষ্কার করে তুলে ধরলে ভয়ে তার বুক কেঁপে উঠবে।
এ দোমনা ও ভীতু মনোভাবের দরুণ প্রাক যুদ্ধের জার্মানি দুষ্ট লোকে ভরে গিয়েছিল। সন্দেহাতীতভাবে এটা জাতির ক্ষয়ের লক্ষণ। যখন মানুষ তার নিজের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সংগ্রামের সাহস হারিয়ে ফেলে, তখন তো তার এ পৃথিবীতে টিকে থাকার সংগ্রাম করার অধিকারই সে হারায়।
পুরনো জার্মানিতে এর একটা বাস্তব চিত্র হল ধীরে ধীরে সংস্কৃতির অবক্ষয়। কিন্তু সংস্কৃতি বলতে আজকের তথাকথিত শাসন যা নাকি সভ্যতা বলে পরিচিত তা বোঝাচ্ছি। বরং এটা আজ জীবনের উন্নতি বলতে যা বোঝায় তার বিরোধী হয়ে দাঁড়িয়েছে।
গত শতাব্দীর মোড় ফেরার সময় পৃথিবীতে একটা নতুন জিনিসের অভ্যুদয় হয়েছে; এ ব্যাপারটা কিন্তু সম্পূর্ণরূপে বিদেশী যা নাকি আমাদের কাছে আগে অজ্ঞাত ছিল। আগে ভাল কোন জিনিস গ্রহণ করাটাকেও দোষণীয় বলে মনে করা হত; কিন্তু ধর্মীয় অনুশাসনের পর থেকে তা অনেক দূরে সরে গেছে। হয়ত ভবিষ্যত পুরুষেরা এর মধ্যে কোন একটা ঐতিহাসিক মূল্য খুঁজে বার করবে। কিন্তু নতুন বংশধরেরা যে শুধু শৈল্পিক সৃষ্টির দিক থেকে বিপথগামী তাই নয়, এর মধ্যে কারো কারো তো আদর্শ বলত কোন অনুপ্রেরণাই নেই। এটা হল সাংস্কৃতিক ধ্বংসের বহিঃপ্রকাশ।
বলশেভিজম মতবাদের বিশ্বাসীদের প্রতিটি শিল্পকর্ম তাদের মতবাদে জারিত এবং পুরো সংস্কৃতিটাই তাদের এ জারক রসে ডোবানো।
যাদের এ বক্তব্যে সন্দেহ আছে তাদের কাছে বিনীত অনুরোধ যেসব রাষ্ট্রে বলশেভিজম প্রচলিত, যদি সেইসব ভাগ্যবান রাষ্ট্রগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে লোকগুলো দেহমনে ব্যাধির দ্বারা কী ভীষণভাবে আক্রান্ত, যা শুধু তাদের পাগল করে তোলেনি, অধঃপাতেও নিয়ে গেছে। এসব শৈল্পিক বিপথগামীতা যা নাকি কিউবিজিম, ডাডজিম, প্রভৃতি নামে খ্যাত, এ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে সেগুলোই হল এসব রাষ্ট্রের বহিঃপ্রকাশ। এমন কি ব্যাভেরিয়ার ক্ষণস্থায়ী সোভিয়েত গণতন্ত্রের সময়ের এ জিনিসগুলোর প্রকাশ ঘটেছিল। সেই সময় অনেকেরই হয়ত বা স্মরণে আসবে সরকারি প্রাচীরপত্র, বিজ্ঞাপন, সংবাদপত্র ইত্যাদিতে শুধু রাজনৈতিক অবক্ষয়ের চিহ্নও কত স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল।
প্রায় বছর ষাটেক আগে আজকের মত রাজনৈতিক ধ্বংস কল্পনাতেও আনা অসম্ভব ছিল। আজকে সাংস্কৃতিক জগতে অবক্ষয় যা নাকি কিউবিস্ট এর ভবিষ্যত ছবিগুলোতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত; ষাট বছর আগে এ ধরনের প্রদর্শনী, যা তথাকথিত ডাডেস্টি সম্পূর্ণ অসম্ভব একটা আদর্শ বলে মনে করা হত। এ ধরনের প্রদর্শনীর ব্যবস্থাপকদেরও জায়গা হত গিয়ে পাগলাগারদে। অথচ আজ তাদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সভাপতির স্থান দেওয়া হচ্ছে। সেই সময়ে এ ধরনের মড়ককে বাড়তে দেওয়া হত না। জনসাধারণ ব্যাপারটাকে কখনোই মেনে নিত না, বা সমকালীন সরকার চুপ করে থাকত না। কারণ এ ধরনের বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন পাগলদের পাগলামী থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করা সরকারের কর্তব্য। কিন্তু সেই বুদ্ধিজীবী পাগলদের পাগলামী এ ধরনের শিল্পকে মেনে নেওয়া ক্রমেই বেড়ে চলেছে; মানবজাতির ইতিহাসে এটা একটা বিরাট পরিবর্তনের নিকৃষ্টতম উদাহরণ। কারণ এর মাধ্যমেই জনসাধারণের বুদ্ধিবৃত্তির পশ্চাদগমন শুরু হয়েছে, যার পরিণতি অচিন্ত্যনীয়।
আমরা যদি আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের গত পঁচিশটা বছর অনুধাবন করি, তাহলে দেখতে পাব সাংস্কৃতিক জগতে কতখানি আমরা পেরিয়ে গেছি। সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যাবে যে এ জীবাণু ছড়িয়ে। সেই সূতীকার বৃদ্ধি আজ হোক কাল হোক আমাদের সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে ছাড়বে। এখানে সন্দেহাতীতভাবে দুর্নীতির স্রোত প্রবাহিত। এবং জাতির পক্ষে এটা মর্মান্তিক যে এ ব্যাধিকে আর থামিয়ে রাখা অসম্ভব।
জার্মান শিল্প এবং সংস্কৃতির প্রায় সর্বক্ষেত্রেই এ রোগ প্রতীয়মান। এখানে সবকিছুই মনে হয় সর্বোচ্চ সীমারেখা অতিক্রম করে দ্রুতগতিতে অবক্ষয়ের দিকে সেই রেখা এগিয়ে চলেছে। শতাব্দীর প্রথমপাদেই নাটকের মান নিচে নামতে শুরু করে, এবং সংস্কৃতির জগতের পটভূমি থেকে দ্রুত সরে যেতে থাকে। এর একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল রাজপ্রাসাদের নাটকগুলো। যা বারবার সাংস্কৃতিক জগতের এ বেশ্যাবৃত্তির বিরোধিতা করে এসেছে। অবশ্য এর সঙ্গে ব্যতিক্রম হিসেবে আরো কয়েকটা মুষ্টিমেয় প্রতিষ্ঠানের নাম করা যেতে পারে। সেখানে এমন কিছু নাটকের অভিনয় হত যে লোকে তা না দেখেও তার থেকে উপকৃত হত। এ অবক্ষয়ের একটা দুঃখজনক উদাহরণ হল অনেক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের প্রবেশ দরজায় লেখা থাকত : প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য।
মনে রাখা দরকার যে এ সব প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যুবকদের ভেতরে শিক্ষাবিস্তার। শুধু সর্বাধুনিক জ্ঞানসম্পন্নদের আনন্দের খোরাক জোগান নয়, অন্যকালের দিকপাল নাট্যকাররা এ ব্যবস্থা সম্পর্কে কি বলত, সর্বোপরি যার জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে, কুপিত হতেন, গ্যেটেও বা বিরক্তিতে কত দূরে সরে যেত।
আমাদের আধুনিক জার্মান সাহিত্যের নায়কদের সঙ্গে কি গ্যেটে বা সেক্সপীয়ারের তুলনা করা চলে? তারা হল প্রাচীন, ছাতাধরা, সেকেলে এবং সর্বোপরি নিঃশেষ। এটাই হল বর্তমান যুগের বিশেষত্ব যে শুধু এ যুগের ফসলই নিকৃষ্ট তা নয়, যারা সেই ফসলের উৎপাদনকারী এবং সেই উৎপাদনের যারা সাহায্যকারী তারাও কম নিকৃষ্ট নয়; যা সত্যই একদিন অতীতে সবদিক দিয়ে মহান ছিল। এ সব যুগের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হল এগুলো। তার চেয়েও অধম এবং ক্লেশক্লিষ্ট হল মানুষ, যারা এসব যুগের ফসল। এরা যত বেশি আগেকার বংশাবলীর কৃতিত্ব অস্বীকার করবে, তত বেশি নিচে নামবে। এদের একমাত্র ইচ্ছে হল পুরনো পদচিহ্নের সমস্ত চিহ্ন পুরোপুরি মুছে ফেলা। এর কারণ আর কিছুই নয়, যাতে কারোর পক্ষে আর তুলনা করা সম্ভব না হয় যে পার্টির নামে তারা সত্যিকারের কি জিনিস নিয়ত পরিবেশনা করে চলেছে। এ কারণেই নতুন দিগন্তের নামে যে সকল এরা উৎপাদন করে চলেছে, তা শুধু জঘন্য নয়, শোচনীয়ও বটে। আর এদের প্রচেষ্টা যাতে পুরনো দিনের স্মৃতি সম্পূর্ণ মুছে ফেলা সম্ভব হয়। কিন্তু সত্যিকারের কোন পরিবর্তন যা মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর, তা সর্বদা অতীতের সঙ্গে তুলনার জন্য প্রস্তুত থাকে। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে পুরনো দিনের স্মৃতি বর্তমানের ফসলকে সাগ্রহে বরণ করে নিতে সাহায্য করে। কারণ সেক্ষেত্রে এমন কোন আশংকা থাকে না যে অতীতের তুলনায় বর্তমানের চিত্র বিবর্ণ এবং অর্থহীন দেখাবে। মানুষের সাংস্কৃতিক জগতের পরিপূর্ণতার সমুদ্রে পুরনো দিনের স্রোত সর্বদাই বরণীয়। কারণ এ স্মৃতিই তো বর্তমান উৎপাদনের নিয়ামকসূচক। একমাত্র তারাই অতীত স্মৃতির কোন মূল্যায়ণ করে না, বরং যে কোন মূল্যে তা ধ্বংস করতে চায়, কারণ তাদের দেখার মত কিছু নেই।
আর উপরের বিষয়টি শুধু সাংস্কৃতিক জগতের পক্ষেই সত্য নয়, রাজনৈতিক জগতেও এ চিরসত্য। নতুন আন্দোলন যত বেশি নিষ্ফলা, ততবেশি অতীত ঐতিহ্যের ধ্বংসের প্রতি তাদের অবহেলা দেখানোর প্রচেষ্টা। এখানে আবার তাদের সেই মনোভাবই সক্রিয়; অর্থাৎ যা পুরাতন কিন্তু সত্যিকারের তাদের উৎপাদিত ফসলের চেয়ে অনেক উৎকৃষ্ট, তাদের বিবেচনায় নিকৃষ্ট। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, যতদিন পর্যন্ত ফ্রেডারিক দ্যা গ্রেটের স্মৃতি থাকবে, ফ্রেডারিক অ্যালবার্ট ততদিন পর্যন্ত দ্বিধা মেশানো বাহবাই পেয়ে আসবে।
সূর্যের সঙ্গে চন্দ্রের যেমন তুলনা, সান্ সুসির নায়কের সঙ্গে ব্রেসেনের ভূতপূর্ব গণতান্ত্রিক নেতার তেমনি তুলনা করা চলে। কারণ সূর্যের আলো আকাশের বুক থেকে মুছে যাওয়ার পরেই একমাত্র চন্দ্রের আলোর প্রকাশের সম্ভাবনা। এ কারণেই মানুষের চন্দ্রিমারা নির্দিষ্ট চিরায়ত গ্রহকে ঘৃণা করে এসেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, ভাগ্য যদি সাময়িকভাবে এদের দেশের শাসন ক্ষমতায় আসতে সাহায্য করে, তবে অতীতকে এরা শুধু কলুষিতই করে না, কৌশলে এড়িয়েও যায়। এ সত্যের একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ হল জার্মান গণতন্ত্রের সংরক্ষণ আইন যা নাকি জার্মান রাষ্ট্র রক্ষার নিমিত্ত করা হয়েছে।
এসব কারণে যে কোন ব্যক্তির পক্ষে সন্দেহ পোষণ করার যথেষ্ট কারণ আছে যে নতুন আদর্শ, মতবাদ বা দর্শন, যে কোন রকমের রাজনৈতিক বা সামাজিক আন্দোলন, যা নাকি অতীতে উৎপাদিত হয়েছে তা বর্তমানের তুলনায় নিকৃষ্ট এবং মূল্যহীন। যে কোন পরিবর্তনের শুরু হয়ে থাকে, যা সত্যিকারের মানবজাতির অগ্রগতির পরিচায়ক, শেষ ধাপে যে পাথরটা গাঁথা হয়েছিল তার থেকে। অতীতের সেইসব প্রতিষ্ঠিত সত্যকে কাজে লাগাবার জন্য লজ্জিত হবার কিছুই নেই। কারণ মানুষের সংস্কৃতির উৎস এবং মানুষ স্বয়ং হল সেই দীর্ঘ উন্নতির সরলরেখার ফসল। যেখানে প্রতিটি বংশাবলী এ বিরাট সৌধ গড়ে তোলার জন্য একটার পর একটা পাথর সাজিয়ে গেছে। বিপ্লবের লক্ষ্য বা মূল উদ্দেশ্য বাড়িটাকে ভেঙে ফেলার নয়; যেসব জিনিস খাপ খাচ্ছে না, অথবা যোগ্য নয়, সেগুলোকে সরিয়ে তার জায়গায় নতুন করে ভিত দিয়ে তারপর সৌধটার নির্মাণ কার্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।
এগুলোকেই একমাত্র মানবজাতির উন্নতি বলা চলে, নইলে পৃথিবীটাকে গোলমালের হাত থেকে কিছুতেই মুক্ত করা সম্ভব নয়; কারণ প্রতিটি বংশাবলী অতীতের কাজকে বাতিল করে দিতে চাইবে, এবং পুরনোকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করবে, আর এটাকেই এরা নতুন কাজ শুরুর প্রাথমিক কর্ম বলে গণ্য করবে।
যুদ্ধের পূর্বে আমাদের সভ্যতার সবচেয়ে দুঃখজনক দিক হল, এর নিজস্ব কোন সৃষ্টির উৎপাদন ক্ষমতা ছিল না যার দ্বারা সাহিত্য বা সভ্যতার কিছু অগ্রগতি হতে পারে; কিন্তু অতীতের উঁচুদরের কার্যাবলীর স্মৃতি এরা মুছে ফেলতে, কলুষিত করতে এবং ঘৃণা করতে আরম্ভ করে। ব্যাপারটা এমন এক জায়গায় এসে দাঁড়ায় যে মনে হয় এ ক্ষয়িত যুগের মহৎ কিছু সৃষ্টি করার ক্ষমতাই নেই। অতীতকে বর্তমানের দৃষ্টি থেকে এমনভাবে গোপন করে রাখা হয় যে মনে হবে ভবিষ্যতের দেবতার পুরো শয়তানের দ্বারা পরিচালিত। এ কার্যকরণগুলো সবার কাছে পরিষ্কার করে দেওয়া উচিত নতুন বলে নয়, এগুলো ভুল বলেই। কিন্তু যে পদ্ধতিতে মানবসভ্যতার ভিত্তি তৈরি করা হয়েছে, সেটাই ঠিক নয়। এ খামখেয়ালি শিল্পই বলশেভিক মতবাদের স্রোতটাকে বয়ে আনতে সাহায্য করে। যদি পেরিক্লিন যুগের সৃষ্টির উন্মাদনা বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত হয়, তবে বলশেভিক তার কিউবিষ্ট বিকৃত মুখভঙ্গি করে হাসাহাসি করবে।
এ প্রসঙ্গে একশ্রেণীর লোকের সাহসের অভাব; বিশেষ করে শিক্ষাদীক্ষা এবং পদমর্যাদার দরুণ তাদের উচিত ছিল আমাদের সাংস্কৃতিক এ চূড়ান্ত অবমাননার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। তারা প্রতিরোধের থেকে সরে দাঁড়ায় কারণ তারা এটাকে অনিবার্য বলে মেনে নিয়ে তার কাছে মাথা নত করেছিল। সুতরাং তাদের এ পদস্থলন প্রাপ্য, কিন্তু তাদের নিছক ভয়ই তথাকথিত বলশেভিক শিল্পের দেবতাদের রাজ্যে গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে। কারণ যারাই তাদের শিল্প সৃষ্টিকে মেনে নিত না, সেই দেবতারা তাদেরই প্রচণ্ডভাবে আক্রমণ করত এবং তাদের ভাষায় এসব মনোবৃত্তি হল সংকীর্ণমনা এবং আবদ্ধ জলা। লোকে আরো ভয় পেত এ ভেবে যে এসব প্রতারক জোচ্চরগুলো তাদের নামে বলে বেড়াবে যে তাদের শিল্পজ্ঞান বলতে কিছু নেই। এগুলো যেন এমন একটা ব্যাপার যা সত্যিকারের ভাবোচ্ছাস আর অধঃপতনের বস্তু যা নাকি কতগুলো কুখ্যাত শঠের সৃষ্ট, তা না বুঝতে পারলে সমাজ তাদের ছোট চোখে দেখবে। এসব সাংস্কৃতিক ভক্ত দলের একটা গুণ ছিল যে সহজ উপায়ে এ ভাবোসগুলোকেই অতি উৎকৃষ্ট ধরনের শিল্প বলে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে পারত। অতুলনীয় এবং চরম মাদকতাময় উপায়ে তাদের সমকালীন শিল্পকে তুলে ধরতে নিজস্ব অন্তরের অভিজ্ঞতা বলে। এ পথেই তারা তাদের বিরুদ্ধে সমালোচনাকে এড়িয়ে যেত অতি অল্প আয়াসে। বলাবাহুল্য, এ অন্তরের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে কেউ-ই কোনরকম সন্দেহ প্রকাশ করত না। কিন্তু সন্দেহ করা উচিত ছিল যে পাগলের সৃষ্টির পেছনের তাগিদটা সত্যিকারের কি? মারটি ভন সুইন্ড অথবা বালনের শিল্পই হল অন্তরের অভিজ্ঞতার সার্থক প্রকাশ; কিন্তু এগুলো হল ঈশ্বরের দান, কোন বিদুষকের কাজ নয়।
আমাদের বুদ্ধিজীবীদের কাপুরুষতার এটা একটা চমৎকার উদাহরণ, যারা নাকি আমাদের মানুষগুলোর সহজাত প্রবৃত্তিকে বিষিয়ে দেওয়াটা কোনরকম প্রতিরোধ ছাড়াই সহজভাবে মেনে নিয়েছে সবরকম নৈতিক দায়িত্ববোধ কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে। এ অবিবেচক অর্থহীন ব্যাপারটাকে লোকের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছে। অর্থাৎ তারা যা ভালো বোঝে তাই করতে। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি জনসাধারণের বিচার ক্ষমতা বলতে কিছুই নেই, কারণ শিল্প জিনিসটাকেও বুঝতে অক্ষম। তারা শিল্পের নামে যে কোন ব্যঙ্গ তামাসাকেও মেনে নিয়ে থাকে; অবশ্যই যতক্ষণ না শেষ পর্যন্ত তারা শিল্পের ভাল বা খারাপ বিচার বোধটাকে হারিয়ে ফেলে।
এসব বিচার বিবেচনা করলে দেখা যাবে অপর্যাপ্ত চিহ্ন সেই যুগে বর্তমান যার দ্বারা সহজেই বোঝা সম্ভব যে পচনক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে।
আরেকটা বিপদজ্জনক চিহ্ন বিচার বিবেচনা করা উচিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের নগর এবং শহরগুলো তাদের সভ্যতা কেন্দ্রিক চরিত্র হারিয়ে ফেলে এবং মাত্র সাময়িক বসবাসকারীর চারিত্রিক রূপ নেয়। আমাদের বড় শহরগুলোতে যেসব শ্রমিকেরা বাস করত, তারা আদৌ সেই শহরগুলোকে মনেপ্রাণে ভালবাসত না। এ অনুভূতির সৃষ্টি হওয়ার পেছনের কারণ হল জায়গাগুলোতে হঠাৎ তারা বসবাস করার সুযোগ পায়, যে কারণে তাদের প্রতি কোন মায়া মমতা সেই বসবাসকারীদের প্রাণে ছিল না। অবশ্য এ অনূভূতির জন্য দায়ী হল সামাজিক কারণগুলো, যে কারণে তারা প্রায়ই বাসস্থান বদল। করতে বাধ্য হত। যে নগরে তারা বাস করত তার প্রতি এ কারণে কোন মমতাই গড়ে ওঠার সুযোগ তারা পেত না। এর আরেকটা কারণ হল আমাদের সাংস্কৃতিক শূন্যগর্ভতা এবং শহর জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা। জার্মানির মুক্তি যুদ্ধের সময়ে আমাদের নগর ও শহরগুলো সংখ্যায় শুধু কম ছিল না, আকারেও ছিল খুবই সীমিত। কয়েকটা যাদের সত্যিকারের বড় শহর বলা চলত সেগুলো ছিল তৎকালীন রাজাদের আবাসস্থল, প্রাসাদ নগরী। সেই কারণে সেখানকার সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার একটা আলাদা মূল্য ও মর্যাদা ছিল। হাজার পঞ্চাশেক অধিবাসী অধুষ্যিত সেই শহরগুলো যা প্রায় তখনকার যে কোন বড় শহরের তুল্য, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির কোষাগারস্বরূপ। তৎকালে যখন মিউনিকে হাজার। ষাটেক বাসিন্দা বাস করত, তখনই মিউনিক জার্মান শিল্পের একটা প্রধানকেন্দ্র বলে বিবেচিত হত। বর্তমানে অবশ্য যে কোন শিল্পাঞ্চলেই তার চেয়ে বেশি লোক বসবাস করলেও তাদের নিয়ে কোন মূল্যবোধ নেই। এগুলো হল কতগুলো বস্তী ও গায়ে গা লাগিয়ে দাঁড়ানো ব্যারাকের সমষ্টি, আর কিছুই নয়। সুতরাং এ অর্থহীন বাসস্থানগুলোর প্রতি যদি কারোর মমতা না গড়ে ওঠে, তবে কারোর পক্ষেই বেড়ে ওঠা সম্ভব নয়। যার নিজস্ব চরিত্র বলতে কিছু নেই এবং যেখানে সাংস্কৃতির কোন ছায়া দুঃখ কষ্টের প্রাচীর ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না।
এটাই সব নয়। বড় বড় শহরগুলোর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সত্যিকারের শিল্পকর্মের সৃষ্টির ফলে স্থানটা মরুভূমি হয়ে দাঁড়ায়। এদের আবহাওয়ায় সেই শিল্প ভারাক্রান্ত শহরগুলোর প্রতিচ্ছায়া স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে। আমাদের বড় শহর গুলোতে সভ্যতার দান বলতে কিছুই নেই। শহরগুলো শুধু অতীতের গৌরব আর ঐশ্বর্যের জোরে। বেঁচে আছে। আমরা যদি শহর মিউনিক থেকে দ্বিতীয় লুইড়ভিগের সমস্ত কিছু তুলে। নেই, তবে দেখতে পাওয়া যাবে এ প্রয়োজনীয় শিল্পকর্ম ছাড়া শহর মিউনিক কত কৃশ হয়ে পড়েছে। বার্লিন বা অন্যান্য বড় বড় শহরগুলো সম্পর্কেও এ একই কথা প্রযোজ্য।
কিন্তু নিচের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর প্রতি লক্ষ রাখা একান্ত প্রয়োজন : আমাদের বড় বড় শহরগুলোর এমন কোন স্মৃতি নেই যা নাকি শহরের সাধারণ বিষয়গুলোর ওপরে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে এবং যা এ যুগের চিহ্নস্বরূপ উপস্থাপনা করা যায়। যদিও সুপ্রাচীন শহরগুলোর প্রত্যেকের গৌরবের স্মৃতিসৌধ ছিল। ব্যক্তিগত সৌধমালা কোন সুপ্রাচীন শহরের শিল্পকর্মের প্রদর্শনী নয়। জনসাধারণের জন্য তৈরি স্মৃতিসৌধই চিরস্থায়ী শিল্পের নিদর্শন, যার প্রভাব ক্ষণস্থায়ী নয়। কারণ এগুলো মুষ্টিমেয় ব্যক্তির সম্পদ প্রদর্শন করে না, এ স্মৃতিসৌধগুলো হল সমাজের গুরুত্ব এবং সংস্কৃতির চিহ্ন। এ স্মৃতিসৌধগুলো বসবাসকারীদের নিজেদের শহরের প্রতি অনুপ্রাণিত করবে, যা নাকি আজ আমাদের ধারণার অতীত। মাঝামাঝি গোছের ব্যক্তিগত মালিকানায় কতগুলো। বাড়ি নাগরিকদের দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হয় না, কিন্তু সমাজের সবার জন্য গড়া স্মৃতিসৌধ প্রতিটি নাগরিকের মন ভরাতে পারে।
আমরা যদি সুপ্রাচীন গণসৌধগুলোর সঙ্গে সেই যুগের ব্যক্তিগত বাড়িগুলোর তুলনা করি, তাদের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারব যে এ কাজগুলোর ব্যাপারে কতখানি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, যার প্রতিচ্ছবি সামাজিক জীবনেও গভীরভাবে পড়েছিল। এগুলো হল পরবর্তী যুগের অগ্রগামিতা।
শুধু বাণিজ্যিক প্রসাদগুলো নয়, মন্দির এবং সাধারণের জন্য নির্মিত অট্টালিকাগুলোও রাষ্ট্রের ছিল, যা সত্যি বিস্ময়কর। সমাজই এ সব বিশাল অট্টালিকার মালিক ছিল। এমন কি রোমের গৌরবের অস্ত-সূর্যের দিনেও ব্যক্তিগত ভিলা বা প্রাসাদে শহরের বিখ্যাত জায়গাগুলো পরিকীর্ণ ছিল না; ছিল মন্দির, স্নানাগার বা হামাম, পয়ঃপ্রণালী এবং রাজপ্রাসাদ। এগুলো সবই ছিল রাষ্ট্রের সম্পত্তি, সুতরাং এককথায় জনসাধারণের তার ওপর পূর্ণ অধিকার ছিল।
মধ্যযুগীয় জার্মানিতেও একই আদর্শকে মেনে চলা হত। যদিও শৈল্পিক দৃষ্টিকোণ ছিল আলাদা। প্রাচীনকালে যে চিন্তাধারা এথেন্স শহরের দূর্গে অথবা প্যানথনে রূপ পেত, আজ তা রূপান্তরিত হয়েছে গথিক ক্যাথিড্রালে। মধ্যযুগীয় শহরগুলোর এ স্মৃতিসৌধগুলো ব্যক্তিগত মালিকানায় নির্মিত ছোট ছোট বাড়িগুলোর মাথা ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে ঢুড়ো আন্দোলিত করত। তাদের প্রাচীর, কাজ এবং ইট তৈরিও ছিল দ্রষ্টব্য। এবং এসব শহরে আজও তারাই প্রধান ভূমিকায় বিরাজ করছে, যদিও দিনে দিনে তারা ফ্ল্যাটবস্তীর জঙ্গলে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। কারণ, তারাই স্থানীয় চরিত্র ও সৌন্দর্য লোকের সামনে উপস্থাপনা করে থাকে। গীর্জা, টাউন হল, আত্মরক্ষামূলক স্তম্ভ প্রভূতিই হল চিন্তাধারার বাইরের প্রকাশ যার তুলনা একমাত্র প্রাচীনকালেই পাওয়া সম্ভব।
আজকের জনতার জন্য নির্মিত বাড়িগুলোর আকার এবং উপাদানের অবস্থা সত্যই শোচনীয়, বিশেষ করে ব্যক্তিগত অট্টালিকাগুলোর তুলনায়।
রোমের মত বার্লিনের ভাগ্যেও যদি একই রূপান্তর হয়, তবে ভবিষ্যত বংশাবলী ইহুদীদের বহুতল দোকান, যৌথভাবে গড়া হোটেলগুলোকেই আমাদের সময়কার সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ বলে ধরে নেব। একমাত্র বার্লিনেই দেখা যাবে তুলনামূলকভাবে বাণিজ্যিক কারণে গড়া বাড়িগুলোর সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে তৈরি বাড়িগুলোর কী প্রচণ্ড তফাৎ।
জনতার জন্য তৈরি অধিকাংশ বাড়ি শুধু অপ্রতুলই নয়, হাস্যকরও বটে। এ সব বাড়িগুলো তৈরির সময়ে এদের স্থায়ীত্বের দিকে নজর দেওয়া হয়নি, সাময়িক প্রয়োজনে নির্মিত হয়েছিল এগুলো। কোন সৎ চিন্তা ভাবনাকেই বাড়িগুলো তৈরির সময়ে ঠাঁই দেওয়া হয়নি। বার্লিনের দুর্গ যখন গড়া হয়েছিল, তৎকালীন চিন্তাধারা সম্পূর্ণরূপে আলাদা ছিল, যখন বার্লিন লাইব্রেরি তৈরি হয়েছিল সেই সময়ের সঙ্গে। একটা যুদ্ধ জাহাজ তৈরির ব্যাপারে যেখানে খরচা পড়ে ষাট লক্ষ জার্মান মার্ক, সেখানে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে তৈরি একটা বাড়ির জন্য তার অর্ধেকও খরচ করা হয় না। কিন্তু সত্যি বলতে কি, যার স্থায়ীত্ব এবং অস্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ আরো অনেক ভালভাবে হওয়া প্রয়োজন। তবু ভেতরটা সাজনোর ব্যাপারে আপার হাউস পাথরের ব্যবহারের পরিবর্তে দেওয়ালগুলো শুধু চুনকাম কার পক্ষে রায় দেয়। অবশ্য একথা বলতে দ্বিধা নেই, যে এ বিষয়ে সংসদের মতামতই সঠিক; কারণ চুনকাম করা মাথাগুলো পাথরের দেওয়ালের সৌন্দর্য বুঝতে সত্যই অক্ষম।
আমাদের সমকালীন শহরগুলোই এমন ধাঁচে গড়ে উঠেছে যে তা সামাজিক চরিত্রের প্রকাশ কোনমতেই করে না। সুতরাং সমাজ যে স্থাপত্যকলার মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে না, এতে আর আশ্চর্যের কি আছে। এভাবে বাস্তবিক আমরা এমন একটা জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হব, যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানা বাসিন্দাদের সঙ্গে তার দেশের প্রচণ্ড রকমের গরমিল থেকে যাবে।
এসব হল আমাদের সাংস্কৃতিক জগতের অবক্ষয় এবং সামাজিক অনুশাসনগুলো ভেঙে পড়ার চিহ্ন। আমাদের দিগন্ত সম্পূর্ণভাবে ছোট ছোট স্বার্থ দ্বারা ঢাকা। সত্যি কথা বলতে কি সেগুলোর কোন উদ্দেশ্যই নেই, একমাত্র টাকা রোজগার করা ছাড়া। সুতরাং এসব ঠাকুরের ভজনা করতে গিয়ে আশ্চর্যের কি আছে যে আমাদের নায়কোচিত গুণগুলো অদৃশ্য হয়ে যাবে। অতীতে যে বীজ বপন করা হয়েছিল বর্তমানে আমরা শুধু তার ফসল কেটে চলেছি।
পূর্ববর্তী যেসব ঘটনাবলী দ্বিতীয় সম্রাটের রাজত্ব ভেঙে পড়ার জন্য দায়ী, সেইগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে নির্দিষ্ট এবং সার্বজনীন মতবাদের অভাবেই এ সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। তার ওপর সামাজিক অবসাদ এবং অস্থিরতা তো ছিলই। বিশেষ করে এ অনিশ্চয়তা প্রচণ্ডভাবে দেখা দেয় যখন একের পর এক জীবন জিজ্ঞাসাগুলোর শুরু হয়, এবং তার প্রতি চূড়ান্ত মনোভাব দেখা যায় এদের। এ খামতির আরো একটা কারণ হল সবকাজ অর্ধেকভাবে করা। শুরু হয় শিক্ষা পদ্ধতিতে, তারপর যে কোন দায়িত্ববোধর প্রতি অনীহা, কাপুরুষের মত শয়তানকে সহ্য করা; এমন কি শেষমেষ ধ্বংসকে পর্যন্ত নীরবে মেনে নেওয়া।
কাল্পনিক মানবতাবাদ একটা স্টাইলে এসে দাঁড়ায়। এ বিপথগামীতার প্রতি আত্মসমর্পণ ও ব্যক্তির প্রতি যুদ্ধং দেহি মনোভাবের কাছে আগামী ভবিষ্যতের লক্ষ লক্ষ মানবতাবোধ উৎসর্গ করা হয়েছে।
প্রাক যুদ্ধের ধর্মীয় অবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে দেখা যাবে সাধারণভাবে বিভক্তিকরণ এ পরিবেশটাকেও বিষিয়ে দিয়েছিল। জাতির একটা বিরাট অংশ জাতীয় পোশাক সম্পর্কে উদাসীন এবং সত্যিকারের আদর্শের প্রতি তাচ্ছিল্যের ভাব তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। এ ব্যাপারে প্রাথমিক প্রয়োজনীয় এটা নয় যে বহু সংখ্যক লোক, তার জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী হল লোকদের উদাসীনতা। যখন খৃষ্টধর্মের দুই সম্প্রদায় এশিয়া আর আফ্রিকার বুকে তাদের ধর্মপ্রচার করে চলেছে, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল খৃষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী শিষ্য জোগাড় করা, কিন্তু এ দুই সম্প্রদায়ই তখন ইউরোপে লক্ষ লক্ষ অনুগামীদের বিশ্বাস হারাচ্ছে। এসব শিষ্যরা তখন তাদের জীবনশক্তির উৎসম্বরূপ যে ধর্ম, তাকে পরিত্যাগ করে চলেছে, অথবা তারা নিজের অভিমত অনুসারে সেই ধর্মকে পরিবর্তন করে চলেছে। বিশেষ করে এর ফলাফল দেশের নৈতিক জীবনে সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়েছে। কারণ কথার সঙ্গে কাজের সামঞ্জস্য না থাকায় খৃষ্টীয় বিশ্বাসের চেয়ে মুসলমান ধর্ম অনেক বেশি পরিমাণে এশিয়া আফ্রিকায় ব্যাপ্তি পেয়েছে।
এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে তথ্য নির্ভর নয় বলে এসব মতবাদ খৃষ্টীয় ধর্মের প্রতি মানুষকে আকর্ষণ করার পরিবর্তে হিংসাকেই প্রশ্রয় দিয়েছে। যদিও মানুষের এ পৃথিবী ধর্ম বিশ্বাস ছাড়া যে কী বস্তুতে পরিণত হতে পারে তা আমাদের ধারণার অতীত। কোন জাতিরই বিরাট অংশ দার্শনিক নয়। জাতির বিরাট একটা অংশের বিশ্বাস জীবনের প্রতি ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে। রকমারী ব্যবস্থা যা নাকি আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের পরিবর্তে তুলে ধরা হয়েছে, তার কোন মূল্য নেই। কিন্তু যদি ধর্মীয় অনুশাসন এবং বিশ্বাস জাতির গরিষ্ঠ অংশ মেনে নেয়, তবে সে মতবাদের ভিতস্থাপনা হয় শক্ত জমিতে। জীবন ধাণের প্রাত্যহিক নিয়মগুলোকে না মেনেও হয়ত কয়েক শো বা হাজার অতি মানব আছেন, যারা তাদের জীবনটাকে কাটিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু বাকি লক্ষ লক্ষ লোকের পক্ষে তা সম্ভবপর নয়। প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা যে বাঁধাধরা খাতে বয়ে চলে, রাষ্ট্রের পথও সেই একই খাতে প্রবাহিত। আরো স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে, ধর্মীয় অনুশাসনগুলোও সেই কারণে প্রয়োজনীয়। সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় মতবাদ হল এমন একটা বস্তু, যার বিশদ ব্যাখ্যার শেষ নেই। একমাত্র মতবাদের মধ্যে আবদ্ধ নেই সেই কারণে এটা সূক্ষ্ম এবং শক্ত একটা রূপ দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া কোনরকম বিশ্বাসই গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। নইলে ধর্মীয় মতবাদ কোনক্রমেই দার্শনিক মতবাদের উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হত না। বরং সোজাসুজি একটা দার্শনিক মতবাদে গিয়ে ঠেকত। সেই কারণে এ মতবাদের ওপর আক্রমণ করা আর রাষ্ট্রের কোন অনুশাসনের প্রতি আক্রমণ একই কথা। তাই এ ধরনের কোন আক্রমণ সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ডেকে আনতে বাধ্য।
রাজনৈতিক নেতাদের ধর্মের মূল্যায়ণ কখনোই এর কোন খামতির দিক বিবেচনা করে করা উচিত নয়। তার বদলে তার চিন্তা করা উচিত এর পরিবর্তে অন্য কিছু যা সত্যিকারের ভাল তার পক্ষে জনমত গঠন করা সম্ভব কিনা যতক্ষণ না পর্যন্ত ভাল, এবং গ্রহণযোগ্য কোন ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া যায়, ততদিন পর্যন্ত একমাত্র বোকা এবং দাগী আগামীরাই প্রচলিত ধর্মের অবলুপ্তি চাইবে।
অবশ্য এটা নিঃসন্দেহে সত্য যারা এ প্রচলিত ধর্মের গতি ব্যাহত করেছে, জাগতিক কিছু প্রাপ্তির জন্য তাদের ক্ষমা করাটা মোটেই উচিত হবে না। কারণ বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের সংঘর্ষ তারাই ডেকে এনেছে। এ সংঘর্ষে বিজয়মাল্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের গলাতেই ঝুলবে। যদিও তা হবে তিক্ত সংঘর্ষের পরে, যাতে ধর্মের ক্ষতি প্রচণ্ডই হবে। কারণ কাছেই ধর্মের উচ্চতা খর্ব হবে যাদের দৃষ্টি বিজ্ঞানের ওপরের স্তর ভেদ করতে অক্ষম।
কিন্তু সবচেয়ে ক্ষতি হয়েছে ধর্মে খাদ মিশিয়ে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে সেটাকে ব্যবহার করে। বরং সোজাসুজিভাবে বলতে হয় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যেই ধর্মটাকে ব্যবহার করা হয়েছে। নিলজ্জ উঁচু গলায় চিৎকার করা মিথ্যুক মানুষগুলো যারা খনখনে গলায় তাদের একরাশ মিথ্যা প্রচার করে চলেছে, যা কাপুরুষ উদ্দেশ্যবিহীন লোকগুলোই শোনে। এরা কিন্তু কোন কারণেই মৃত্যুর জন্য তৈরি নয়। বরং কি করে ভালভাবে বাঁচা যায়, তার ফন্দি-ফিকির খুঁজতেই তারা সদাসর্বদা ব্যস্ত থাকে। রাজনৈতিক লাভের জন্য তারা তাদের যে কোন বিশ্বাসকে বিকিয়ে দিতে পারে। মাত্র দশটা সংসদীয় আদেশের জন্য মার্কসবাদীদের সঙ্গে হাত মেলাতে এতটুকু ইতস্তত করে না। যারা হল ধর্মের শত্রু, আর একটা মন্ত্রীত্বের জন্য তারা শয়তানের সঙ্গেও বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হতে প্রস্তুত। যদিও সেই শয়তানের চক্ষুলজ্জা বলতে কোন বস্তু নেই।
প্রাক্ যুদ্ধের জার্মানিতে খৃষ্টধর্মের আস্বাদন বহু লোকের কাছে বিস্বাদ ঠেকে। তবে তার জন্য দায়ী রাজনৈতিক দলগুলো, যারা ক্যাথলিক বিশ্বাসকে লজ্জাস্করভাবে নিজেদের দলীয় স্বার্থে কাজে লাগিয়েছিল।
এ পরিবর্তিত ব্যবস্থাটাই ছিল মারাত্মক। এটা গোটা কয়েক মূল্যহীন সংসদীয় আদেশ পাটির জন্য জোগাড় করতে সমর্থ হয়েছিল; কিন্তু তার জন্য চার্চের ক্ষতি হয়েছিল প্রচণ্ড রকমের।
এ ঘটনার ফলাফল জাতিকেই বহন করতে হয়েছিল। ধর্মীয় জীবনে অবসাদ নেমে এসেছিল, যার ফলে সমস্ত রকম বিশ্বাসের নৈতিকতার প্রচলিত আচার আচরণের ভীত নড়ে উঠেছিল-যা যে কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে।
তবু এসব চিড় খাওয়া ফাটল ধরা সামাজিক সংগঠনগুলো হয়ত খুব একটা ক্ষতিকারক ছিল না, যদি তার ওপর দুঃখের বোঝা আর না চাপানো হত। কিন্তু জাতির কাধে এ ঝড় এমন এক সময় এসে উপস্থিত হয়েছিল যখন অন্তর্দেশীয় একতার প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশি।
রাজনীতির ক্ষেত্রেও পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল জার্মান রাষ্ট্রের কাঠামোর কয়েকটি ব্যতিক্রম যা নাকি আগামী ধ্বংসটাকে দেখিয়ে দিয়েছিল, যদি সময় মত সেগুলোকে শুদ্ধিকরণ করা না হয়। জার্মান নীতির অন্ধত্ব বৈদেশিক এবং অন্তর্দেশীয় প্রায় সবার চোখে ধরা পড়েছিল। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল বাইরে থেকে ছন্দোবদ্ধ মনে হলেও এ ব্যাপারে বিসমার্কের মতামতটাই সত্য, যে রাজনীতি হল সাম্ভব্যতার শিল্প। কিন্তু পরের চ্যান্সেলারদের থেকে বিসমার্কের চিন্তাধারা কিছুটা আলাদা ধরনের ছিল। আর এ পার্থক্য থাকার দরুন বিসমার্কের পক্ষে এ তত্ত্বের নির্যাস তার রাজনীতিতে অভীষ্ট পূরণের জন্য সবরকম রাস্তা দেখা উচিত; অন্তত চেষ্টা করা উচিত। চেষ্টার প্রয়াস থাকার দরকার। কিন্তু তারা পরবর্তী উত্তরাধিকারীগণ এ কথার একটা অর্থই করেছিল যে রাজনীতিতে কোনরকম আদর্শ বা লক্ষ্যের প্রয়োজন একেবারেই নেই। সবচেয়ে বড় কথা তল্কালীন জার্মান রাজনৈতিক নেতাদের কোন দূরদর্শী নীতি ছিল না; কারণ হল পুরো ব্যাপারটাই নড়বড়ে ভিতের ওপরে দাঁড়ানো; বিশেষ করে আন্তর্জাতিকতাবাদের। শুধু তাই নয়, এসব নেতাদের রাজনীতির বিবর্তন সম্পর্কে কোন ধ্যান-ধারণাই ছিল না, যেটা রাজনৈতিক নেতাদের অবশ্যই থাকা উচিত।
তৎকালীন অনেকেই যারা পুরো ব্যাপারটাকে হতাশার দৃষ্টিতে দেখত, তারা দোষারোপ করত যে আদর্শ এবং দিগদর্শনের অভাবেই জার্মান রাষ্ট্রের এ দুরবস্থা। তারা এজন্য দায়ী করত ভেতরের দুর্বলতা এবং আদর্শের অনুর্বরতাকে। যাদের দ্বারা সরকার পরিচালিত, তাদের ধ্যান-ধারণার চিন্তানায়ক হুসটন স্টুয়ার্ট চেম্বারলিন, আজকের যারা প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা তাদের থেকে আলাদা ছিল। আসলে এ লোকগুলো তাদের সময়কালের উন্নতির জন্য চিন্তা করতে অন্যের উপদেশ নিতেও তাদের অহংকারে বাজত। গুস্তোভাস্ অ্যাডফুসের মৃত্যুর পর সুইডিস্ চ্যান্সেলার অস্পেনস্ট্যারিন কিছু সত্যের সন্ধান দিয়েছিল যা নাকি স্মরণাতীত কাল পর্যন্ত সত্য ছিল। সে বলেছিল এ পৃথিবীর শাসন একমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই করা সম্ভব। সুতরাং আশা করা যায় সংসদীয় সদস্যদের ভেতরে এর একটা অণু হলেও থাকা উচিত ছিল। কিন্তু জার্মানিতে গণতন্ত্র প্রবর্তিত হওয়ার পরে এক যৎকিঞ্চিত দেখা পাওয়া যায়নি। তার জন্যই তাদের গণতন্ত্রের রক্ষার আইন পাশ করতে হয়েছে, যার দ্বারা স্বাধীন কোন মতবাদ ব্যক্ত করাই নিষিদ্ধ। অস্পেনস্ট্যারিনের পক্ষে এটা সৌভাগ্য বলতে হবে যে সে তক্কালে জীবন ধারণ করেছিল, এ গণতন্ত্রের কালে নয়।
ইতিমধ্যেই যুদ্ধের আগে এ প্রতিষ্ঠানের শক্তিশালী জার্মান রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করা উচিত ছিল,-সংসদ, জার্মান রাষ্ট্রসভা কিন্তু রাষ্ট্রের পর্যায়ে সবচেয়ে দুর্বলতম স্থান বলে ইতিমধ্যেই পরিচিতি লাভ করেছিল।
সবচেয়ে নোংরা একটা কথা যা এখন শোনা যায় যে বিপ্লবের সময় থেকে জার্মান সংসদীয় গণতন্ত্র আর কার্যকরী নয়। এ কথায় এ ধারণাই সবার হবে যে বিপ্লবের ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অন্যরকম ছিল। কিন্তু বাস্তবে সত্য হল দেশকে টেনে নিচে নামানো ছাড়া অন্য কাজ এ তথাকথিত সংসদীয় প্রতিষ্ঠানের ছিল না। জার্মানির পতনের জন্য এ প্রতিষ্ঠানও কম দায়ী নয়।
এ বিশাল বিধ্বংসকারী শয়তানের দল যারা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে সংসদে ভিড় করেছিল, এরা হল এ সংসদের একটা টিপিক্যাল উদাহরণ, যাদের কোন যুগেই দায়িত্ববোধ বলে কিছু থাকে না। যে শয়তানের কথা আমি বলছি, তা অন্তর্দেশীয় শাসনভার ঢিলেঢালা এবং বৈদেশিক নীতিতেও দৃঢ়তা ছিল না; এগুলোই হল রাজনৈতিক বিপর্যয়ের প্রধান কারণ।
সংসদীয় সমস্ত কাজই অর্ধেক করা হয়েছে এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এ কাজ সম্পূর্ণ না করার নীতি সব ব্যাপারেই মেনে চলা হয়েছে।
মৈত্রীর ব্যাপারে জার্মান রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি একেবারেই নিকৃষ্টতম। তাদের ইচ্ছে ছিল শান্তি স্থাপনের, কিন্তু সোজা গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছে যুদ্ধে।
পোল্যান্ডের ব্যাপারেও এ বৈদেশিক নীতি মনপ্রাণ দিয়ে লাগানো হয়নি। যার ফলে
পেরেছে জার্মানি যুদ্ধে জিততে অথবা পোল্যান্ডকে টেনে নিজের স্বপক্ষে আনতে, বরং রাশিয়াকে শত্রু বানিয়ে ছেড়েছে।
অ্যালসেস-লোরাইনের প্রশ্নটাকে সমাধান করার চেষ্টা করা হয়েছিল মাত্র, কিন্তু পুরোপুরি মন ঢেলে দেওয়া হয়নি। ফরাসী বহু মস্তক বিশিষ্ট জলচর সাপটার মাথা চূর্ণ করার পরিবর্তে শুধু আস্তে একটু ছোঁয়া এবং অ্যালসেস-লোরাইনের তত্ত্ব অনুসারে অন্যান্য জার্মান প্রদেশের সঙ্গে সমান অধিকার মেনে নেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোন ক্ষেত্রেই তারা এক নয় একের সঙ্গে আরেক জনের তুলনা করা চলে না। যাহোক এছাড়া তাদের অন্য কোন গতিও ছিল না, কারণ দেশের মধ্যে তারাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বাসঘাতক; বিশেষ করে মিষ্টার ভিটারলে তো কেন্দ্রের মধ্যমণি।
তবু দেশ এ সব পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারত, যদি না, তাদের সেই প্রতিরোধ করার শক্তিটাকে দোদুল্যমান নিয়তির দ্বারা হত্যা না করা হত। আর এটাই ছিল শেষ পন্থা; সম্রাটের অস্তিত্ব নির্ভর করে তার সৈন্যবলের ওপর।
তৎকালীন জার্মান রাষ্ট্র জাতির প্রতি যে অপরাধ করেছে তাকে নিচে নামিয়ে নিয়ে এসে তার জন্য সারাজীবন জাতির অভিশাপ তাদের প্রাপ্য। এ সংসদীয় দলের সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল এদের রাজনৈতিক সমর্থক দ্বারা এরা জাতির আত্মরক্ষার সবচেয়ে বড় অস্ত্রটাকে অপহরণ করে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। যার জন্য জাতির অস্তিত্ব, স্বাধীনতা সবকিছুই বিপন্ন হয়ে পড়েছে। আজ যদি কবর খোঁড়া হয়, তবে রক্তস্নাত সেইসব ফরিয়াদীরা বেরিয়ে পড়বে, হাজার হাজার জার্মান যুবকের ভবিষ্যতের জন্য দায়ী এ সব রাজনৈতিক ডাকাতগুলো অথবা স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে তাদের ভুল শিক্ষা আর কুশিক্ষাই দায়ী। এ লক্ষ লক্ষ লোকের নিধন বা অঙ্গ ছেদন করা হয়েছিল মাত্র কয়েকশ লোকের রাজনৈতিক কৌশলে ও জোর করে তাদের উপর রাজদ্রোহাত্মক মতবাদ চাপিয়ে দেওয়ার জন্য।
মার্কসবাদী এবং গণতান্ত্রিক সংবাদপত্রগুলো দ্বারা ইহুদীরা সারা পৃথিবীতে জার্মান সামরিক বাহিনী সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার করে। কিন্তু আমাদের জাতীয় বাহিনীর শিক্ষা ব্যবস্থা যে অপ্রতুল, তার কোন ব্যবস্থাই মার্কসবাদী বা গণতান্ত্রিক দলগুলো করেনি। এ ভয়াবহ অপরাধের জন্য যুদ্ধের সময়ে প্রত্যেকের ডাক পড়ে, কারণ এ লোকগুলোর ফেরিওয়ালা মনোবৃত্তির জন্য লক্ষ লক্ষ জার্মানকে তার জন্য অনেক নিম্নমানের অস্ত্রশস্ত্র এবং অর্ধেক সময়ে-ডিক্ষা নিয়ে অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সামরিক শিক্ষায় পারদর্শী শক্রর মুখোমুখি হতে হয়। নির্দয় নিষ্ঠুর রকমের বিবেক-বুদ্ধির অভাবও এ সংসদীয় বদমায়েসদের কম ছিল না। এবং এটা পরিষ্কার যে সুশিক্ষিত সৈন্যের অভাবই এ যুদ্ধে পরাজয়ের অন্যতম কারণ। এবং মহাযুদ্ধের কালে এ সত্যই অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রকাশ পায়।
সুতরাং জার্মান জাতি স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষমতাটাই হারিয়ে ফেলে, কারণ আর কিছুই নয় সংঘের শান্তিবাদী নীতি এবং জাতির আত্মরক্ষার নীতির শিক্ষার অভাব।
পদাতিক সৈন্যবাহিনীতে শিক্ষাপ্রাপ্ত সৈনিক খুব কম পরিমাণেই সগ্রহ করা হয়েছিল এবং সেই নৌ-বাহিনীর অবস্থাও ছিল তথৈবচ। সুতরাং জাতির আত্মরক্ষার অস্ত্রটাকে এভাবে ভোতা করে দেওয়া হয়েছিল। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক যে নৌ-বাহিনীর পদস্থ অফিসাররাও এর জন্য দায়ী। বৃটিশদের থেকে ছোট যুদ্ধ-জাহাজ জলে ভাসাবার মনোবৃত্তি দূরদৃষ্টির পরিচয় নয়। এক সারি জাহাজ বলেই তা কখনো একক জাহাজের যুদ্ধ শক্তির সমতুল্য হতে পারে না। যুদ্ধ করার ক্ষমতাটাই যুদ্ধ করার সময়ে একমাত্র বিবেচ্য। সত্যি বলতে কি, আধুনিক সমর-বিজ্ঞান এত বেশি উচ্চস্তরে পৌঁছেছে যে একই মাপের যুদ্ধ-জাহাজের যুদ্ধ করার ক্ষমতা অন্য দেশের তৈরি সেই মাপের যুদ্ধ-জাহাজের থেকে অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন করা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে; অন্য দেশের বড় যুদ্ধ জাহাজের তুলনায়।
সত্যি কথা বলতে, কি গতি এবং সমর-সজ্জার পরিবর্তে একমাত্র জার্মান নৌ-বহরের ক্ষুদ্র একটা অংশকেই প্রতিপালন করা যেতে পারে। এ নীতির সার্থকতা সম্পর্কে যেসব যুক্তি উপস্থাপনা করা হয়েছে তাতেই প্রমাণিত হয় যে শান্তির সময়ে নৌ বাহিনীর অফিসারদের চিন্তাধারা কতখানি আসার ছিল। তারা ঘোষণা করেছিল জার্মান কামানগুলো বৃটিশ ৩০.৫ সেন্টিমিটার কামানের চেয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে আঘাত করার ব্যাপারে অনেক বেশি কুশলী।
এবং এ যুক্তির জোরেই তারা ৩০.৫ সেন্টিমিটার কামান তৈরি করতে শুরু করে। কিন্তু ওদের উচিত ছিল সমর-সজ্জায় বৃটিশের সমকক্ষ না হয়ে যুদ্ধের অধিক পারদর্শিতা লাভের প্রচেষ্টা করা। যদি এটা সত্যি না হয় তবে বৃথাই তারা পদাতিক বাহিনীকে ৪২ সেন্টিমিটার মটারে সাজিয়েছিল। কারণ জার্মান ২১ সেন্টিমিটার মটারগুলো ফরাসী মটারের থেকে অনেক উন্নতমানের ছিল এবং দুর্গগুলোকে ৩০.৫ সেন্টিমিটার কামানের গোলা দ্বারাই অধিকার করা যেত। কিন্তু সৈন্যবাহিনীর কর্তৃপক্ষের স্থানীয় ব্যক্তিরা এ বিষয়ে কৃতকার্যতা লাভ করতে পারেনি। পদাতিক বাহিনীর অস্ত্রসজ্জায় উন্নত না করার প্রচেষ্টা আর কিছু নয়, মিথ্যা দায়িত্বের ভয়। নৌ-বহর তো শান্তির সময় থেকেই আক্রমণ বিমুখ মনোবৃত্তি নিয়ে বসে ছিল, যার জন্য যুদ্ধের শুরুর থেকেই তারা আত্মরক্ষামূলক নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু এ পথে তারা জয়ের পথ থেকে সরে দাঁড়ায়, কারণ একমাত্র এগিয়ে যাবার নীতিতেই জয়লাভ করা সম্ভব।
নিম্নগতি সম্পন্ন এবং দুর্বল সমরসজ্জা বিশিষ্ট যে কোন যুদ্ধ-জাহাজ তার থেকে দ্রুতগতি সম্পন্ন এবং সমরসজ্জায় সজ্জিত জাহাজের কাছে পঙ্গু এবং আঘাত খেতে বাধ্য, কারণ তাদের পক্ষে দুর্বল জাহাজে একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের বাইরের থেকে আঘাত করা সম্ভব। এক বৃহৎ সংখ্যার ক্রুজারকে এ অভিজ্ঞতার পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। নৌ বহরের অফিসারদের ধারণা যে কত ভুলে ভর্তি ছিল যুদ্ধের সময়ে তা ভালভাবেই প্রমাণিত হয়। তারা বাধ্য হয়ে পুরনো জাহাজগুলোর সমর ব্যবস্থার বদলি করে এবং সুযোগ মত নতুন জাহাজের সমর ব্যবস্থাও উন্নত করতে বাধ্য হয়। যদি জার্মান নৌ বহরের যুদ্ধ-জাহাজগুলো এবং কামানের শক্তি বৃটিশ বহরের যুদ্ধ-জাহাজের অনুরূপ হত-তবে কাগরেকের যুদ্ধে ইংরেজ নৌ-বহর জার্মান ৩৮ সেন্টিমিটার শেষে ধ্বংস হয়ে যেত, যদি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে সঠিক নিশানায় আঘাত করতে পারত।
জাপান অবশ্য নৌ-যুদ্ধের নীতি অন্যরকমের নিয়েছিল। তারা প্রতিটি যুদ্ধ জাহাজ শক্তিশালী করেছিল যাতে বিরুদ্ধপক্ষের যুদ্ধ-জাহাজগুলো এককভাবে এদের শক্তির সঙ্গে পাল্লা দিতে না পারে। এবং এ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যই পরে এগুলোকে আত্মরক্ষার কাজেও লাগানো সম্ভব হয়।
এটা সত্যই অদ্ভূত যে পুরনো জার্মানির দোস ত্রুটিগুলোকেই জনসমক্ষে এমনভাবে তুলে ধরা হয় যাতে তার অন্তর্নিহিত ঐক্যে চিড় খায়। এমনকি অপ্রিয় সত্য বাক্যগুলো সরবে বারবার বিশাল জনতার কানে তুলে দেয়া হয়েছে; কিন্তু অন্যান্য বহু জিনিস চাপা দিয়ে দেওয়া হয়েছে বা ইচ্ছাকৃতভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। বিশেষ করে সেই খোলাখুলি বিতর্ক যখন জাতির উন্নতিকে টেনে আনার সম্ভাবনায় রয়েছে। সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ এ ব্যাপারে হয় কিছুই অবহিত ছিল না। বা সামান্যই খবর রাখত। একমাত্র ইহুদীরাই জানত প্রচারের সেই আর্ট যার দ্বারা স্বৰ্গকেও নরক বলে তুলে ধরা যায় অথবা তার উল্টোটা। সবচেয়ে দুঃখজনক ক্লেশময় জীবনকেও স্বর্গীয় বলে মনে হত এদের প্রচারের ধরন-ধারণে। ইহুদীরা অভিনয়ও করত সেই ঢঙে। কিন্তু জার্মান, বিশেষ করে জার্মান সরকার এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করত না। যুদ্ধের সময়ে এ অজ্ঞতার জরিমানা যথেষ্ট পরিমাণেই দিতে হয়েছিল।
অসংখ্য দোষের মধ্যে যা আমি উল্লেখ করেছি, যুদ্ধ পূর্ব জার্মানির ভাগ্যে বহু লাঞ্ছনা ডেকে এনেছে, তার একটা ইতিবাচক দিকও ছিল। যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে পুরো ব্যাপারটাকে বিচার করি তবে দেখতে পাব অন্য দেশ এবং জাতির মধ্যেও এ দোষ বর্তমান। আমাদের থেকে তা অনেক গভীরে। উপরন্তু আমাদের যত সুযোগ ছিল, অন্য কারোরই তা ছিল না।
জার্মানির ইতিবাচক দিকটার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল জার্মানির অর্থনৈতিক শক্ত বুনিয়াদ, যা অপর কোন ইউরোপীয় দেশের ছিল না। সেই কারণে অন্য দেশের আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করা তার পক্ষে সহজ ছিল। যদিও স্বীকার করতে বাধা নেই যে এর মধ্যে খুঁতও কম ছিল না। তবু এ আধিপত্য বিপদজ্জনকও বটে। এটাই ভবিষ্যত বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
এমন কি আমরা যদিও জাতির স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অগ্রাধিকার দিতে স্বীকারও না করি, তবু রাজনৈতিক এবং সামাজিক ব্যাপারে এর ভুমিকা যে অত্যন্ত চমকপ্রদ তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এ বিষয়গুলোই তিনটে প্রতিষ্ঠানকে উপস্থাপন করত। যারা নিয়মিত পুনঃঅভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে শক্তি জোগাত।
প্রথমদিকে তো জার্মানির আধুনিকীকরণের ব্যাপারে রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করেছে। সুতরাং আমাদের সেইসব রাজাদেরও মেনে নেওয়া উচিত তাদের কাজের গলতির জন্য আজকের গণজীবন এবং সন্তানদের জীবন দুঃখ জর্জরিত হয়ে পড়েছে। আমাদের যদি এসব ব্যাপারে সহনশীলতা না থাকে, তবে বর্তমান যুগের ছেলেরা হতাশ হয়ে পড়বে। সমকালীন কালের প্রতিনিধিদের চরিত্র, ব্যক্তিগত দক্ষতার কথা যদি বিচার করি তবে দেখতে পাব তাদের বুদ্ধিমত্তা এবং নৈতিক চরিত্রের মানদণ্ড খুব একটা উঁচু ছিল না। আমরা যদি জার্মান বিপ্লবের ব্যক্তিগত মূল্যায়ণ করি, তবে দেখব ১৯১৮ সালের বিদ্রোহ সাধারণ জীবনের কোন উন্নতি সাধনই করেনি। এবং উত্তরকালের বংশধরেরা কী ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে পথ হাঁটবে যখন জার্মান সংরক্ষণ আইনের দ্বারাও তাদের মতামত চাপা দেয়া যাবে না।
আজকের রাজনৈতিক নায়কদের বুদ্ধিমত্তা, নীতিজ্ঞান বিচার করে আগামী বংশধরেরা তাদের সম্পর্কে নিচু ধারণাই পোষণ করত।
এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বেশির ভাগ জনতার কাছে সেই রাজা বিদেশী বলেই পরিগণিত হত। এর কারণ আর কিছুই নয়, রাজাদের বুদ্ধিমত্তা সব সময় সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল না এবং আরো স্পষ্ট ভাষায় বলা যায় চারিত্রিক দৃঢ়তা হয়তবা ছিল না। দুর্ভাগ্যবশত বেশির ভাগ রাজাই তোষামোদপ্রিয় ছিল এবং এসব চাটুকারের দলই তাদের গোপন খবরাখবর দিত।
শতাব্দীর শেষে একজন যুবরাণীকে ঘোড়ার পিঠে চড়ে সৈন্য পরিদর্শন করতে দেখে জনসাধারণের মধ্যে আর আগেকার মত চাঞ্চল্য জাগত না। তৎকালীন উঁচুতলার বাসিন্দাদের এটাও জানা ছিল না যে এ ধরনের প্যারাড সাধারণ মানুষের ভেতরে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া জাগায়। যদি ধারণা থাকত তবে হয়ত বা এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটত না। ভাবালুতাসম্পন্ন মানবতাবাদ—যার সঙ্গে বেশিরভাগ সময়েই অন্তরের স্পর্শ থাকে, তৎকালে এ ওপর তলার বাসিন্দাদের আচ্ছন্ন করে রেখেছিল; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা জনসাধারণকে আকর্ষণের পরিবর্তে বিকর্ষণই করত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ক’ রাজা যদি মুরগীর স্যুপ খেয়ে ভাল বলত, সবারই ভেতরে তার সেই তৃপ্তিটা ছড়িয়ে পড়ত; কিন্তু তা হত আজ থেকে অনেক আগে; আজ তা আর নেই। বরং পুরো ব্যাপারটাই উল্টে হয়ে গেছে। যদি আমরা এটা ধরেও নেই যে রাজা মহারাজাদের এসব ব্যাপারে একেবারেই কোন ধ্যান-ধারণা ছিল না, তবু এটা স্বীকার করেত হবে যে তাদের বোঝা উচিত ছিল দিনকাল বদলে গেছে। এমনকি তাদের সবচেয়ে ভাল উদ্দেশ্যটাও হাস্যকর লাগত অথবা ক্রোধের কারণ হয়ে দাঁড়াত।
সুবিদিত মিতব্যয়িতা যার মধ্যে সেই সব রাজাদের দিন কাটত, তাকে খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে গভীর রাত পর্যন্ত একঘেয়ে কঠোর খাটতে হত, বিশেষ করে সদা সর্বদা তার মুকুট হারানোর আশঙ্কায়। সব মিলিয়ে লোকদের পক্ষে পুরো ব্যাপারটাই অমঙ্গল সূচক ছিল। রাজারা কতখানি খায় বা পান করে, এ সব বিষয়ে কারোরই কোন আগ্রহ ছিল না; সে পরিপূর্ণ খেল কিনা বা প্রয়োজনের পরিমাপ মত ঘুমল কিনা, এসব বিষয়ে কারোরই কোন প্রকার মাথাব্যথা ছিল না। রাজা তার ব্যক্তিত্বের জোরে যখন তার পরিবারের সম্মান নিয়ে আসত এবং যে সম্মান দেশেরও বটে; দেশের সার্বভৌমত্ব বজায় রাখার ব্যাপারে তার কর্তব্য করে যেত। তার সম্পর্কে যত সব গল্প কথা প্রচারিত হত, তা’ তার লক্ষ্যে পৌঁছতে সাহায্য খুব কম পরিমাণেই করত, বরং ক্ষতি করত অনেক বেশি।
অবশ্য এসব ব্যাপারগুলো একরকম খেলা ছাড়া কিছু নয়। সবচেয়ে খারাপ ছিল সেই সময়কার বিশেষ একটা অনুভূতি যে ব্যক্তিগত সবার স্বার্থ রাজা নিপুণ হাতে দেখছে এবং জনসাধারণের বিরাট একটা অংশ এ চিন্তাতেই নিশ্চিত ছিল। সুতরাং তাদের নিজস্ব স্বার্থের ব্যাপারগুলো নিয়ে তারা মোটেই ভাবিত ছিল না। যতক্ষণ দেশে ভাল সরকার প্রতিষ্ঠিত, অন্ততপক্ষে সৎ চিন্তার দ্বারা সেই সরকার সুপরিচালিত, ততদিন পর্যন্ত তো কোনরকম প্রতিবাদ উঠতে পারে না। কিন্তু যখন পুরনো সরকারের বদলে নতুন সরকার দেশের শাসনভার তুলে নেয়, যার দক্ষতা মোটেই পূর্বের সরকারের মত নয়, তখনই দেশ বিপর্যয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়ায়। শান্ত, বাধ্যতা এবং নির্দয়তার শৈশবস্থা যা আগের সরকারের প্রতি কোন প্রতিবাদ তোলেনি, তা সমাজের পক্ষে রীতিমত বিপদজ্জনক হয়ে দাঁড়ায় যা নাকি কল্পনাতেও আনা যায় না।
কিন্তু এসব এবং অন্যান্য দোষ ছাড়াও তাদের নিশ্চয়ই কিছু গুণ ছিল যার প্রভাব ইতিবাচক।
প্রথমত রাজতন্ত্র জনসাধারণের ব্যাপারেও তাদের স্বার্থরক্ষায় স্থির প্রত্যয় সরকার, বিশেষ করে আন্দোলনকারী উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজনৈতিক নেতাদের থেকে এসব ব্যাপারে তাদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল অনেক বেশি। উপরন্তু সুপ্রাচীন অভিযানগুলোও এ সব রাজতন্ত্রের মহিমা বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করত। তার চেয়েও বড় কথা সৈন্যবাহিনী এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দকে রাজনীতির উর্ধে সবসময় রাখা হত। দেশের সর্বোচ্চ শাসনভার রাজার ওপরেই ন্যস্ত থাকত। সত্যি কথা বলতে কি, সুবিদিত সাধুতা এবং জার্মান শাসনকার্যে অখণ্ডতা প্রধানত এ কারণেই বজায় ছিল। শেষমেষ রাজতন্ত্রের কারণে জার্মান জনসাধারণের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক প্রসার লাভ করে, তা’ এর অনেক দোষত্রুটি ঢাকতেই সাহায্য করেছিল। আমাদের সময় পর্যন্ত জার্মান শহর সংস্কৃতি এবং শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল; যা নাকি চরম বস্তুতান্ত্রিক হয়ে উঠেছে। জার্মান যুবরাজরা বারবার বিজ্ঞান এবং শিল্পকলার উৎকর্ষতার জন্য উৎসাহ দিয়ে এসেছে। সমকালীন যুগে এর কোন তুলনা নেই।
ধীরে ধীরে সামাজিক বিপর্যয়ের সময়ে এ সৈন্যদলই সবচেয়ে বেশি প্রতিরোধ করেছিল। জার্মান জনসাধারণের এর চেয়ে ভাল শিক্ষা আর জোটেনি বললেই হয়। এ কারণেই শত্রুদের সব ঘৃণা আমাদের জাতীয় সংরক্ষণ ও স্বাধীনতা নামক মল্লবীরের বিরুদ্ধে বর্ষিত হয়। এ প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আমাদের সবচেয়ে বড় সুশিক্ষা হল এদের পি, ভয় এবং ঘৃণা; আন্তর্জাতিক মুনাফাখোরের দল যারা ভার্সালেসে জড়ো হয়েছিল জাতিকে লুণ্ঠন এবং প্রতারণা করার জন্য, তাদের সমস্ত শক্রতার লক্ষ্য ছিল প্রাচীন জার্মান বাহিনী যারা নাকি ফাটকার হাত থেকে জাতিকে এতদিন বুক দিয়ে রক্ষা করে এসেছে। যদি এ সৈন্যবাহিনী জাতীয় স্বার্থ এত নিপুণ হাতে না দেখত তবে ভার্সাইয়ের প্রতিনিধিবৃন্দ অনেক আগেই তাদের স্বার্থ কার্যে পরিণত করত। একমাত্র একটা শব্দের দ্বারা এ সৈন্যবাহিনীর কাছে জার্মানদের কি ঋণ প্রকাশ করা হয়, তা হল-সবকিছু।
যখন লোকদের ভেতরে এ গুণের অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে, সবাই যে যার দায়িত্ব কাঁধ থেকে ছেড়ে ফেলে দিতে উৎসুক, তখন সামরিক বাহিনী তাদের কর্তব্য স্থির প্রতিজ্ঞভাবে পারলন করে চলেছে। এবং একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে গণতন্ত্রের ঝড়ো আবহাওয়ায় তাদের এ দায়িত্ববোধ সযত্নে পালন করে চলেছে। সামরিক বাহিনী জনসাধারণকে সাহসী হতে শিক্ষা দিয়েছিল যখন ভীরুতায় সমস্ত জনসাধারণ ভুগছে এবং তা মহামারীরূপে দেখা দিয়েছে। তখন সমাজের মঙ্গলের জন্য কারোর ব্যক্তিগত স্বার্থ ত্যাগটাকে পাগলামী বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। তখনকার যুগে যখন একমাত্র চালাক ব্যক্তিরাই নিজেদের স্বার্থরক্ষা করত, তখন সামরিক বিভাগই ছিল একমাত্র বিভাগ, যা নাকি জাতির মুক্তির পথ বাতলে দিয়েছে মিথ্যা আদর্শের মায়ায় আকৃষ্ট করে আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃভাবে নিগ্রোদের, চাইনিজ, ফ্রেঞ্চ বা ইংরেজদের সঙ্গে জার্মানদের শেখায়নি। তাদের শিক্ষা ছিল নিজেদের জাতিকে একতা ও দৃঢ়তার বন্ধনে বাঁধা।
সামরিক বাহিনী একতা শক্তিকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করতে সাহায্য করেছে, তখনকার সময়ে যখন সন্দেহবাদ দোষে সামগ্রিকভাবে মানুষের চরিত্র দুষ্ট এবং পণ্ডিত-মূর্খের দল নকল ফ্যাসানের আদর্শে নিজেদের আবৃত করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, যে কোনরকম আদেশ পালন করা কোন কিছু না করার চেয়ে অনেক ভাল। যদিও এটাকে ভাসা ভাসাভাবে স্থির প্রতিজ্ঞ ও শক্তিশালী একটা আদর্শ বলে মনে হয়, তবু সামরিক বাহিনী যদি নিয়মিত জীবনে যৌবন না জুগিয়ে যেত তবে এ ভিত্তি আদর্শের কোন প্রাণ নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যেত না। এ ব্যাপারে অনেক ভয়াবহ খামতির পরিচয় পাওয়া যায়, যা নাকি আমাদের বর্তমান সরকারের কার্যকলাপে প্রকট। তাদের ভেতরে নতুন কাজকর্মের দরুন কোনরকম উৎসাহের সাড়া বর্তমানে নেই, অবশ্যই তা যদি জার্মান জাতিকে প্রতারণার ব্যাপারে না হয়। এ ব্যাপারে অবশ্য তাদের সমস্ত দায়িত্ববোধ তারা ঝেড়ে ফেলে দেয় এবং দলিলপত্রে স্বাক্ষর দেয় এমন ভঙ্গিতে যেন সরকারি আমলামাত্র। তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে যে তাদের মতামত দেবার কোন ক্ষমতাই নেই, মতামত জোর করে তাদের ওপর চেপে বসানো হয়েছে।
সারাদেশ জুড়ে যখন চলছিল লোভ লালসা আর জড় রাজ্যের প্রাধান্য, তখন সামরিক কর্তৃপক্ষ সেনাবাহিনীর সদস্যদের এক আদর্শবাদে দীক্ষিত করে তোলে। সে আদর্শ হল দেশের প্রয়োজনে জীবন বিসর্জনের জন্য সবসময় প্রস্তুত থাকতে। এ সেনাবাহিনী বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত দেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে। সেদিক দিয়ে এর একটা দোষ ছিল। দেশে সামরিক শোধনবাদের সুযোগ থাকতে দেয় না। একসময় যারা এ চিন্তা থেকে মুক্ত তারাই সে সুযোগ পেত। এটা দোষ, এজন্য যে এর দ্বারা দমনের নীতিটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। কারণ এর ফলে যারা বেশি শিক্ষা লাভ করেছে তাদের সাধারণ মানুষের স্তর থেকে সরিয়ে এনে সম্পূর্ণ পৃথক এক উন্নত স্তরে আবদ্ধ করে রাখা হত। এর উল্টোটা হলেই বরং ভাল হত। যেহেতু আমাদের উচ্চ অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা জাতির জীবনে কি ঘটছে না ঘটছে সে সম্বন্ধে কিছুই জানত না এবং এভাবে তারা জনগণের জীবন থেকে ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছিল। সেই হেতু সেনাবাহিনী যদি নিজেদের মধ্যে ভেদজ্ঞানের পরিচয় না দিত, যদি বুদ্ধিজীবীদের বেশি সুযোগ সুবিধে না দিত, তাহলে তারা দেশের অনেক উপকার সাধন করতে পারত। এ বিষয়ে অবশ্যই তারা ভুল করেছিল। কিন্তু সমগ্র জাতির মধ্যে এমন কি কোন প্রতিষ্ঠান আছে যার মধ্যে ভুল ত্রুটি নেই। কিন্তু আমাদের সেনাবাহিনীর দোষত্রুটিগুলো চোখেই পড়ত না। মানবজাতির দুর্বলতাজনিত সাধারণ দোষত্রুটির তুলনায় তা অনেক কম।
কিন্তু আমাদের সেনাদলের সবচেয়ে বড় প্রসংশার কাজ হল মানুষের সমষ্টিগত মূল্যায়নের ওপরে ব্যক্তিগত মূল্যায়ণকে স্থান দেওয়া। ইহুদি ও গণতন্ত্রের প্রবক্তাদের সংখ্যাদিক্যপ্রিয়তা ও মানুষের সংখ্যাগত শক্তির ওপর অত্যধিক নির্ভরতার নীতিতে বাধা দিতে থাকে। তখন আমাদের দেশের যার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল তা সত্যিকারের মানুষের; আমাদের সেনাবাহিনী সুকঠোর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানুষের মত মানুষ গড়ার কাজে ব্রতী হয়েছিল। দেশের মানুষ যখন নারীসুলভ দুর্বলতা ও আলস্যে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল, তখন প্রতি ঘরের থেকে একজন করে সর্বসাকুল্যে সাড়ে তিন লক্ষ সামরিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবক সেনাবাহিনী থেকে বেরিয়ে এসে জনগণের সঙ্গে মিশে যেত। তাদের এ দুটি বছরের প্রশিক্ষণকালে তারা সমস্ত দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে ইস্পাতের মত শক্ত করে তুলত তাদের দেহগুলোকে। দু’টি বছর ধরে যেসব যুবক চরম আনুগত্য শিক্ষা করে আসত, প্রশিক্ষণ পেয়ে তারা পরিচালনা কার্যের যোগ্য হয়ে উঠত সর্বতভাবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিককে তার চলন দেখেই চেনা যেত।
এ সেনাবাহিনীই ছিল সমগ্র জার্মান জাতির সবচেয়ে বড় শিক্ষালয়। এভাবে নিতান্ত সঙ্গত কারণেই আমাদের সেনাবাহিনী সেই ব্যক্তির ঘৃণার বোঝা মাতায় তুলে নিয়েছিল, যারা চাইত জার্মান সাম্রাজ্য প্রতিরক্ষাহীন অবস্থায় দুর্বল হয়ে যাক; এরা নিজেরা লোভ লালসায় জর্জরিত বলে জার্মান জাতির উন্নতিতে ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠেছিল। যে কথা সমগ্র জগৎ বুঝতে পেরেছিল সেকথা অনেক জার্মান বুঝতে পারেনি, কারণ তারা দেখে শুনে অন্ধ হয়েছিল অথবা হিংসার বশে সেকথা বুঝতে চায়নি। বাধা হল এ যে জার্মান জাতির স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার এবং দেশের নাগরিকদের জীবিকার্জনের ক্ষেত্রেও এ উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতির প্রতীক।
তার মধ্যে যে প্রতিষ্ঠানের নাম করা যেতে পারে, রাজশক্তি ও সেনাবাহিনীর ওপরে যাকে স্থান দেওয়া যেতে পারে, তা হল জার্মান সিভিল সার্ভিস বা অসামরিক প্রশাসন ব্যবস্থা।
জার্মানির শাসনব্যবস্থা অন্যান্য দেশের শাসনব্যবস্থার থেকে আরো উন্নত ও সুগঠিত। সরকারি কর্তাব্যক্তিদের আমলাতান্ত্রিক রাজনীতির বিরুদ্ধে অনেক আপত্তি থাকতে পারে, কিন্তু সে রাজনীতি অন্যদেশের তুলনায় এমন কিছু বেশি খারাপ নয়। অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রশাসনযন্ত্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে জার্মানির মত এমন ঐক্য ও অখণ্ডতা নেই। তাছাড়া জার্মানির মত অন্যান্য রাষ্ট্রের সিভিলসার্ভিসের আমলাদের মধ্যে এতখানি সততা ও নৈতিক কুণ্ঠা নেই। অহংকারী, অসৎ, দুশ্চরিত্র ও অযোগ্য সরকারি কর্মচারীদের থেকে সৎ মনোভাবাপন্ন আমলা অনেক ভাল। কেউ যদি বলেন প্রাকযুদ্ধকালীন জার্মানির শাসনব্যবস্থায় আমলারা সৎ হলেও প্রশাসনিক কাজকর্মের দিক থেকে তারা ছিল অযোগ, তাহলে আমি নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করব;
পৃথিবীর আর কোন্ দেশে জার্মানির থেকে আরও উন্নত ও সুগঠিত প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল? দৃষ্টান্ত স্বরূপ স্টেট রেলওয়ের উল্লেখ করা যেতে পারে। তারপর বিপ্লব এসে এ প্রশাসন ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার করে দেয়। ক্রমে এমন একদিন আসে যেদিন এ বিপ্লবের কর্ণধার পুঁজিবাদীরা জার্মানির প্রশাসন যন্ত্রটাকে আন্তর্জাতিক শিল্পপতিদের দ্বারা পরিচালিত স্টক এক্সচেঞ্জের নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসে।
বিপ্লবের সময় সিভিল সার্ভিসের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল অসৎ মনোভাবসম্পন্ন সরকারি কর্মচারীদের অবাধ স্বাতন্ত্র। দেশের প্রচলিত রাজনৈতিক আবহাওয়া জার্মানির সরকারি কর্মচারীদের ওপর কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারে না। বিপ্লবের পরে সমগ্র পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন হয়। কর্মচারীদের যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতার জায়গায় পার্টি আনুগত্য স্থান গ্রহণ করে। চরিত্রের স্বাধীনতা ও কর্মতৎপরতা সরকারি কর্মচারীদের আদর্শ গুণ হিসেবে আর স্বীকৃত হয় না। বরং এ সব গুণগুলি ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে তাদের পক্ষে।
আগে জার্মান সাম্রাজ্যের আশ্চর্যজনক বিশাল শক্তিটি প্রতিষ্ঠিত ছিল রাজতন্ত্রের ওপর। আর এ রাজতন্ত্রের নির্ভরযোগ্য ভিত ছিল সেনাবাহিনী ও সিভিল সার্ভিস। এ তিনটি ভিতের ওপর রাষ্ট্র কর্তৃত্বরূপ শক্তির যে বিশাল সৌধটি প্রতিষ্ঠিত ছিল আজ তা দেখা যায় না। পার্লামেন্ট বা প্রাদেশিক সভাগুলোর কাজকর্মের দ্বারা কখনো রাষ্ট্রের কর্তত্ব বা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। কোন দেশের সরকার ও শাসন কর্তৃপক্ষ জনগণের মনে যে বিশ্বাস উৎপাদন করে তাদের সততা ও কর্মদক্ষতার দ্বারা, সে বিশ্বাসই হল রাষ্ট্র কর্তৃত্বের মূল ভিত। দেশের সরকার ও শাসন কর্তৃপক্ষ এক নিঃস্বার্থপরতা ও সততার আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করছে। এ ধরনের এক অটল অবস্থা থেকেই জনগণের বিশ্বাস উৎপন্ন হয়। শুধু সন্ত্রাসের দ্বারা কখনো কোন সরকারের শাসনব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখা যায় না; জনগণের উন্নতিতে তৎপর শাসন কর্তৃপক্ষের যোগ্যতা ও নিষ্ঠায় জনগণের যে বিশ্বাস-সেই বিশ্বাসই কোন সরকারের শাসনব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে পারে। অবশ্য একথা সত্য যে প্রাকযুদ্ধকালীন জার্মানিতে এমন কিছু অসভ্য শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটে শাসনব্যবস্থার মধ্যে, যা জাতির অন্তনিহিত শক্তিকে জোরদার করে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে জার্মানির তুলনায় অন্যান্য রাষ্ট্রে এ ধরনের শক্তির কর্মতৎপরতা আরো বেশি। এ কথাটায় বুঝতে পারব আমাদের ধ্বংসের মূল কারণটা কোথায়।
জার্মানির পরাজয়ের প্রধানতম কারণ হল এ যে জার্মানিতে বর্ণসমস্যা এবং জাতির ঐতিহাসিক বিবর্তন ধারার এ সমস্যার তাৎপর্যটিকে উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করা হয়। কারণ মনে রাখতে হবে কোন জাতির জীবনে যে সব ঘটনা ঘটে তা কখনো দৈবক্রমে ঘটে না, তা হল জাতিরই কার্যের স্বাভাবিক প্রতিফল। জাতির জনসংখ্যা কিভাবে বেড়ে চলেছে এবং জাতীয় শক্তির সংরক্ষণ কিভাবে হচ্ছে তারই ওপর নির্ভর করছে জাতির ভবিষ্যত।
————–
* ৩৯০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সীনেনিয়ন গলরা আলিয়ার যুদ্ধে রোমান সৈন্যদের সম্পূর্ণ পরাস্ত করে এবং শহর রোমে প্রবেশ করে দেখে শহরটা মরুভূমি প্রায়, শুধু ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরা সাগ্রহে অপেক্ষা করছে। যাদের আশা নিজেদের উৎসর্গ করে হলেও দেশকে রক্ষা করা। সদস্যরা আদেশ দেয় তাদের হাতির দাঁতের চেয়ারগুলো মন্দিরের সামনে রাখতে, এবং এরপর তারা যে যার চেয়ারে বসে; চেয়ারের সঙ্গে নিজেদের বেঁধে রেখে বিজয়ী সৈন্যদের জন্য অপেক্ষা করে। লিবির ভাষায়, গলরা যখন শহরে ঢোকে, দেখে মাননীয় সদস্যরা চেয়ারে উপবিষ্ট। একদল অবতার যেন তাদের জন্যই অপেক্ষা করছে। স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে শহর রোম রক্ষার নিমিত্তে। মহৎ উদ্দেশ্য সন্দেহ নেই; যদিও আক্রমণকারীদের হাত থেকে এর দ্বারা শহর রক্ষা করা যায়নি। তবু পরবর্তীদের পক্ষে এটা একটা মহৎ উদাহরণ।
১০. বর্ণ ও জনতা
কতগুলি সত্য আছে যা মানুষের পথের ধারে এমন সহজভাবে ছড়িয়ে থাকে যে তা প্রতিটি পথিকেরই চোখে পড়ে। কিন্তু তাদের সর্বদাই দেখা যায় বলেই মানুষ সেই সব সত্যগুলোকে বুঝতে বা তাদের বিশেষ বিষয়বস্তু বলে গণ্য করতে চায় না। সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনের কতগুলো অতি সরল ও সাধারণ ঘটনা সম্বন্ধে এমনি অবহিত যে যখন কেউ সেই বিষয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষন করে তখন আশ্চর্য হয়ে যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কলম্বাস ও ডিমের ঘটনাটার উল্লেখ করা যায়। ঘটনাটি খুবই সহজ, সকলেই তা জানে। কিন্তু কলম্বাসের মত পর্যবেক্ষক সত্যই বিরল।
প্রকৃতির বাগানে বেড়াতে বেড়াতে অনেকে অহংকারের সঙ্গে ভাবে তারা প্রকৃতির সবকিছু জেনে গেছে। কিন্তু তাদের কেউ-ই প্রকৃতির জগতের এক বিশেষ নীতির কথা জানে না। সে নীতি হল এ যে জগতের সকল জীবন্ত প্রাণীর মধ্যেই এক বিচ্ছিন্নতাবোধ নিহিত আছে।
এ নিয়মের বশেই প্রতিটি প্রাণী তার আপন জীবন বৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ থেকে তার প্রজাতি বৃদ্ধি করে চলে। প্রতিটি প্রাণী তার স্বজাতীয় স্ত্রী প্রাণীর সঙ্গে সহবাস করে থাকে। যেমন ঘরের ইঁদুর কখনো মেঠো ইঁদুরের সঙ্গে সহবাস করে না। সে কাজে তার একমাত্র সঙ্গী ঘরের ইঁদুর। নেকড়ের স্ত্রী নেকড়ের সঙ্গেই সহবাস করে।
একমাত্র বিশেষ অবস্থার বশেই প্রাণীরা এ যৌন প্রকৃতির নিয়ম হতে বিচ্যুত হতে বাধ্য হয়। কোন জায়গায় বন্দী থাকাকালীন অথবা যখন স্বজাতীয় প্রাণীর সঙ্গে কোনক্রমে সহবাস সম্ভবপর হয় না, তখনি কোন প্রাণী ভিন্ন জাতীয় প্রাণীর সঙ্গে বাধ্য হয়ে সহবাস করে থাকে। কিন্তু এ ধরনের সহবাস প্রকৃতি ঘৃণা করে এবং এর বিরুদ্ধে প্রকৃতির নীরব প্রতিবাদ বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমে পরিব্যাপ্ত হয়। যেমন ভিন্ন জাতির দুই প্রাণী হতে উৎপন্ন বর্ণসংকর কোন প্রাণী সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকভাবে প্রজনন ক্ষমতা হতে বঞ্চিত। এ বর্ণসংকর কোন প্রাণীর অনেক রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা ও বহিরাক্রমণ হতেও আত্মরক্ষার ক্ষমতায় বঞ্চিত হয়।
প্রকৃতির এ বিধান খুবই যুক্তসঙ্গত। দুটি অসম স্তরভুক্ত ভিন্নজাতীয় প্রাণী তার পিতামাতার থেকে কিছুটা উন্নত হলেও তাদের থেকে উন্নত কোন প্রাণীর আক্রমণে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে না। এ কারণেই ভিন্ন জাতীয় দুই প্রাণীর সহবাস প্রাণধারার নির্বাচন যুক্ত বিবর্তন সম্পর্কিত প্রকৃতির ইচ্ছার সম্পূর্ণ বিরোধী; বলবান প্রাণীও দুর্বল দুই ভিন্ন জাতীয় প্রাণীর মিলন প্রাণের উন্নত বিবর্তনধারার পরিপন্থী। কারণ এসব সহবাসের ক্ষেত্রে বলবান প্রাণীকে কিছুটা নতি স্বীকার করতে হয় এবং এ মিল হতে যে প্রজাতির জন্ম হয়, তার প্রকৃতি ও মান দুর্বল হয়। সুতরাং এক অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা প্রাণের বিবর্তনধারাটা নিয়ন্ত্রণ না হলে জৈব জীবনের উন্নয়নমূলক বিবর্তন মোটেই সম্ভব হত না।
অমিশ্রিত রক্তবিশিষ্ট অর্থাৎ সমজাতীয় দুই প্রাণীর মিলনের এ নীতিটি তাই প্রকৃতি জগতের সর্বত্র পালিত হয়, এবং এ মিলনের ফলে যে প্রাণীর জন্ম হয় তা শুধু দেহগত আকৃতি নয়, চরিত্র ও স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অন্য জাতীয় প্রাণী হতে সম্পূর্ণ পৃথক হয়। শেয়াল ও বাঘের চরিত্র কখনো কি এক হবে? তাদের জাতীয় চরিত্র ভিন্ন থাকবেই। শেয়াল কখনো রাজহাঁসের প্রতি আর বিড়াল কখনো ইঁদুরের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন হতে পারে না।
প্রকৃতি আবার প্রতিটি জাতির জীবনধারাকে উন্নত করার জন্য প্রতিটি জাতির প্রাণীদের মধ্যে ক্ষুধা ও প্রেমগত প্রতিযোগীতা ও জীবন সংগ্রামের এক তাগিদ সঞ্চারিত করে দিয়েছে। দৈনন্দিন জীবিকার্জন ও স্ত্রী প্রাণীদের ওপর অধিকার ও কর্তৃত্ব নিয়ে সমজাতীয় প্রাণীরা ঝগড়া ও সংগ্রাম করে পরস্পরের মধ্যে। সংগ্রামে বলবানরাই প্রাধান্য লাভ করে দুর্বলের ওপর।
তা’ যদি না হত তবে বিভিন্ন জাতীয় প্রাণীদের উন্নতির বা বিবর্তনের ধারাটা বন্ধ হয়ে যেত একেবারে। তাহলে অগ্রগতির পরিবর্তে শুরু হত পশ্চাদ্গতি। প্রাণীদের মধ্যে যারা দুর্বল, যারা অযোগ্য, তারা সংখ্যায় বেশি। তারা যদি অবাধে যা ইচ্ছেমত বংশবৃদ্ধি করে যেতে পারে তাহলে সব জাতির প্রাণীর মধ্যে অযোগ্য ও দুর্বলের সংখ্যা বেড়ে যাবে। তাদের মধ্যে ভাল গুণগুলো কমে যাবে। তাই অযোগ্য ও দুর্বলদের সংখ্যাকে সীমায়িত ও তাদের অবাধ বংশবৃদ্ধিকে খর্ব করার জন্য প্রকৃতি এমন এক কঠোর নির্বাচনমূলক নীতি ও নিয়মের প্রবর্তন করেছে, যার ফলে প্রজননের ক্ষেত্রে অযোগ্য ও দুর্বলদের সব সময় স্বাস্থ্যবান ও শক্তিমানদের কাছে নতি স্বীকার করে চলতেই হবে।
|||||||||| প্রকৃতির রাজ্যে এ নিয়ম যদি প্রতিষ্ঠিত না থাকত, যদি যোগ্য-অযোগ্য, দুর্বল ও শক্তিমান অবাধে সহজভাবে মেলামেশা করত, তাহলে প্রকৃতি শত শত হাজার হাজার বছর ধরে সকল জাতির প্রাণীর বংশধারাটিকে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে উর্ধ্বতন স্তরের দিকে নিয়ে যাবার যে প্রমাণ পাচ্ছে, সে প্রমাণ ব্যর্থ হয়ে যেত।
ইতিহাসের মধ্যে এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যার মধ্যে এ প্রকৃতির নিয়মটি অভ্রান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে। ইতিহাসে দেখা যায় যে আর্যরা একদিন এক উন্নত ধরনের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক ছিল, সেই আর্যদের রক্ত যখন নিকৃষ্ট জাতির রক্তের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়, তখন তাদের পতন ঘটতে থাকে। উত্তর আমেরিকার অধিবাসীরা ছিল প্রধানত টিউটন জাতীয়। কিন্তু তারা যখন নিকৃষ্ট জাতির লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করতে থাকে তখন তারা মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার অধিবাসীদের থেকে পৃথক হয়ে পড়ে, এবং তাদের সভ্যতার মান কমে যায়। মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার লাতিন জাতীয় অধিবাসীরা আবার অদিবাসীদের রক্তের সঙ্গে তাদের রক্ত বহু পরিমাণে মিলিয়ে ফেলে। বিভিন্ন জাতির রক্তগত সংমিশ্রনের ফল কি হতে পারে তা আমরা এ দৃষ্টান্ত থেকে বেশ বুঝতে পারি। কিন্তু উত্তর আমেরিকার নিউটনজাতীয় যেসব লোকেরা তাদের জাতিগত সত্তা ও রক্তের পবিত্রতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়, যারা তাদের রক্তকে অন্য জাতির রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেনি, তারাই সমগ্র আমেরিকার ওপর কর্তৃত্ব করতে থাকে এবং তাদের রক্ত সংমিশ্রিত বা দূষিত না হওয়া পর্যন্ত তারা এভাবে প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব করে যাবে।
জাতিগত সংমিশ্রণের কুফল সাধারণত দু’ভাবে দেখা যেতে পারে;
(ক) উৎকৃষ্ট জাতির গুণগত মান কমে যায়;
(খ) তাদের দৈহিক ও মানসিক ক্রমাবনতির জন্য তাদের প্রাণশক্তি কমে গিয়ে শুকিয়ে যেতে থাকে।
জাতিগত রক্তের এ দুষণ ক্রিয়া পরম স্রষ্টার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক ঘোরতর পাপ এবং এ পাপের ফলভোগ করতেই হবে।
মানুষের এ কাজ যেসব নীতির ওপর তার অস্তিত্ব নির্ভর করে, সেইসব নীতির বিরুদ্ধে সংঘাতে প্রবৃত্ত করে তোলে তাকে। এভাবে প্রকৃতির বিরুদ্ধাচারণ করে সে নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে আনে।
এ বিষয়ে ইহুদি ও আধুনিক শান্তিবাদীদের কাছ থেকে এক ঔদ্ধতামূলক আপত্তির সম্মুখীন হই। তারা বলেন, মানুষ প্রকৃতির ওপর প্রভুত্ব করতে পারে। ইহুদীদের অনুসরণ করে বহু লোক এ ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করে যে তারা প্রকৃতিকে জয় করতে পেরেছে। কিন্তু এটি শুধু তাদের এ বিপজ্জনক ধারণামাত্র। কারণ তাদের এ বিপদজনক ধারণাটাকে যদি সকলে স্বীকৃতি দান করে তাহলে জগতের অস্তিত্বই একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।
আসল কথা এ যে মানুষ প্রকৃতিকে যে কোন ক্ষেত্রে জয় করতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রকৃতি যে বিশাল অবগুণ্ঠন বা আবরনের দ্বারা তারা অন্তর্নিহিত গোপন রহস্যগুলোকে অনন্তকাল ধরে ঢেকে রেখেছে, মানুষ শুধু সেই অবগুণ্ঠনের সামান্য এক অংশমাত্র অপসারিত করতে পেরেছে। মানুষ কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। সে শুধু কিছু আবিষ্কার করতে সক্ষম। মানুষ প্রকৃতিকে জয় করতে পারে না, তারা শুধু সেই সব প্রাণীদের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে পেরেছে যারা প্রকৃতির নিয়ম কানুন ও রহস্যের গভীরে প্রবেশ করার মত উপযুক্ত জ্ঞান অর্জন করতে পারেনি। যে কোন ভাব বা ধারণার জন্ম হয় মানুষের মনের মধ্যে। তাই মানব জাতির অস্তিত্ব রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য যে সব ঘটনা অত্যাবশ্যক, সেই ঘটনাগুলিকে কোন ভাব বা ধারণা কখনো ধ্বংস করতে পারে না। মানুষকে দিয়ে কোন ভাব বা ধারণা কখনো জন্মলাভ করতে পারে না। সুতরাং যে কোন ভাব বা ধারণা মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য অবশ্যই সেই ঘটনাগুলোর ওপরে নির্ভরশীল হবে।
শুধু তাই নয়। কতগুলো ভাব বা ধারণা আবার কতগুলো মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিশেষ করে যেসব ভাব বা ধারণা একান্তভাবে অনুভূতি সম্পন্ন। যেগুলো বস্তু সাপেক্ষ বৈজ্ঞানিক সত্য হতে উদ্ভূত নয়, সেগুলোর ক্ষেত্রে একথা সমধিক প্রযোজ্য। অনেকে বলে এ সব ভাবগুলো নাকি মানুষের অন্তরঙ্গ জীবনের প্রতিফলন। তাদের মত এসব আত্মগত ভাবগুলোর নীরস যুক্তিতর্কের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। এগুলো মানুষের নৈতিক ধারণার প্রকাশ মাত্র। তারা আরও বলে মানুষের অন্তরে সৃষ্টিশীল শক্তিই এ সব ভাবগুলোর উত্স। বিশেষ তাবধারা বা ধারণাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে সেই বিশেষ জাতিকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ; যদি কেউ মনে করে শান্তিবাদী ভাবধারার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত, তাহলে তাকে জার্মান জাতির বিশ্বজয়ে সর্বপ্রকার যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত। এর উল্টোটা হলে সমগ্র জার্মান জাতির সঙ্গে সব শান্তিবাদীদেরও মরতে হবে। আমি একথা বলছি কারণ দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের জার্মান জাতি এ ভাবধারার অধীন হয়ে পড়ে। কেউ যদি শান্তিবাদী আদর্শে দীক্ষিত হতে চায় তাকে তবে যুদ্ধের কথা একেবারেই ভুলে যেতে হবে। আমেরিকার বিশ্ব-সংস্কারপন্থী নেতা উড়া উইলসনের এ ধরনের এক পরিকল্পনা ছিল। এ আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে আমাদের দেশের অধিবাসীরাও ভাবত এ পরিকল্পনার মাধ্যমেই তারা তাদের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারবে।
শান্তিবাদ ও মানবতাবাদ এক উক্তৃষ্ট ভাবাদর্শ হিসেবে বিবেচিত হবে সেইদিন, যেদিন মানুষ পৃথিবীতে পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ করবে এবং সেই মনুষ্যত্ব এক অবিসম্বাদী প্রাধান্য বিস্তার করবে সারা বিশ্বে। কিন্তু কেউ যদি অপরিণামদিৰ্শতার বশে এ ভাবাদর্শ জোর করে কারোর ওপর চাপাতে চায়, তবে তা ক্ষতিকারক হয়ে উঠতে বাধ্য। তাই চাই আগে যুদ্ধ, তারপরে শান্তি। যদি তা না হয় তাহলে বুঝতে হবে মানুষ আগেই উন্নতির সব পথ বন্ধ করে দিয়েছে। অপরিণামদর্শিতার বশে এ ভাবধারা চালিত করলে নৈতিক আদর্শ এবং প্রাধান্য স্থিতি হবে না; বরং মানুষ নিচুস্তরে নেমে যাবে। আর তার ফলে ব্যাপক বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে সারা বিশ্বে। এ কথায় অনেকে হয়ত হাসতে পারে। আমাদের এ পৃথিবীর মানুষ আমাদের আগে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মহাশূন্যে একা একা ঘুরে চলেছিল। ভবিষ্যতে কোনদিন আবার হয়ত তাকে সেভাবে জনমানবশূন্য অবস্থায় ঘুরতে হবে, যদি মানুষ একথা ভুলে যায় যে স্বপ্নপ্রবণ অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তিত্বের ভাবধারাকে ভিত্তি করে নয়, প্রকৃতির নিয়ম কঠোরভাবে মেনে তবেই মানুষ বড় হতে পারে; যে কোন জায়গায় তারা তাদের অস্তিত্বকে সমৃদ্ধ ও মহান করে তুলতে পারে।
আমরা সারা বিশ্বের বিজ্ঞান, কলা ও কারিগরী বিদ্যার যে সব আবিষ্কার ও উন্নতির প্রশংসা করি তা মুষ্টিমেয় কিছু লোকের সৃষ্টিশীল প্রতিভার ফল। জাতিগত ভিন্নতা সত্বেও এসব প্রতিভাবান ব্যক্তিরা বুদ্ধিগত যোগ্যতার দিক থেকে যেন একই জাতীয়। মানব সভ্যতার অস্তিত্ব আসলে এসব প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের ওপরেই নির্ভরশীল। এসব ব্যক্তিত্বের ধ্বংস হলে পৃথিবীর যা কিছু সুন্দর তা’ সব তাদের সঙ্গে চলে যাবে ধ্বংসের সমাধিগহ্বরে।
কোন দেশের ভূ-প্রকৃতির প্রভাব যতই বেশি হোক সে প্রভাব নির্ভর করে সে দেশের অধিবাসীদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের ওপরে। কোন দেশের ভূমির পরিমাণ কম হলে সে দেশের মানুষেরা খুব পরিশ্রমী হয়, ভূমির অভাব অন্যদিক থেকে পুরণের চেষ্টা করে। আবার কোন কোন দেশে দেখা যায় ভূমির অভাবের ফলে সে দেশের লোকেরা চরিত্র হারিয়ে ফেলে এবং স্বাভাবিকভাবেই অপুষ্টি প্রভৃতি দারিদ্র্যগত কুফলগুলোয় ভুগতে থাকে। সুতরাং কোন দেশের অধিবাসীদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যই পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও পরিবেশ প্রভাবের গতি প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। কোন দেশের ভূমির ঘাটতি জাতিকে দারিদ্রতা ও অনশনের পথে ঠেলে দেয়, আবার অন্য এক জাতিকে কঠোর পরিশ্রমের পথে নিয়ে যায়।
অতীতের বড় বড় সভ্যতার ধ্বংসের কারণ হল প্রতিভাবান শ্রেণীর রক্তে সংমিশ্রণ ও দূষণের ফলে অবনতি ঘটে এবং তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।
এ সব ধ্বংসের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ তখনকার মানুষ একটা কথা ভুলে গিয়েছিল; ভুলে গিয়েছিল সকল সভ্যতা ও সংস্কৃতি সেইসব মানুষের ওপরে নির্ভরশীল যারা সেই সব সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্রষ্টা। সুতরাং কোন সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে তাদের স্রষ্টাদেরও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এ বাঁচিয়ে রাখার নীতির সঙ্গে আর একটা অমোঘ নীতি জড়িয়ে আছে, সে নীতি হল এ যে যারা অধিকতর শক্তিমান ও যোগ্যতম তাদের প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা স্বীকার করতেই হবে। তাদের বেঁচে থাকার অধিকার দিতেই হবে।
এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে হলে লড়াই করতে হবে। যে পৃথিবীতে নিরন্তর সংগ্রামই জীবনের নীতি ও নিয়ম, সেই পৃথিবীতে কেউ যদি লড়াই করতে না চায়, তার বেঁচে থাকার কোন অধিকারই নেই।
একথা রূঢ় শোনালেও প্রকৃত অবস্থা এটাই। তবে তাদের অবস্থা আরো খারাপ হয়ে ওঠে যারা প্রকৃতিকে জয় করার দম্ভ দেখিয়ে প্রকৃতিকে অপমান করে। ফলে তাদের ভাগ্যে ঘটে অশেষ দুঃখকষ্ট।
বিভিন্ন জাতির রক্তগত প্রকৃতিক নিয়মকে কেউ যদি উপেক্ষা বা ঘৃণা করে তাহলে সম্ভাব্য সুখ থেকে বঞ্চিত করবে নিজেকে। যোগ্যতম ব্যক্তিত্বের জয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করে এ ধরনের ব্যক্তিরা সমগ্রভাবে মানবজাতির উন্নতির পক্ষে আবশ্যকীয় বস্তুগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। মানবতাবাদের এবং ভাবালুতার বশবর্তী হয়ে তারা আবার মানুষের স্তরে নিজেদের নামিয়ে নিয়ে যায়, যারা ভেবেছিল নিজেদের তুলে নিয়ে যেতে পারবে না কোন উন্নতির স্তরে।
মানবজাতির প্রথম সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক কারা ছিল এবং তারা কোন জাতিভুক্ত ছিল, সেকথা আলোচনা অর্থহীন। আজ আমরা মনুষ্যত্ব বলতে যা বুঝি, আমাদের সে ধারণা একদিন তারাই বপন করেছিল আমাদের মনে। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আজ খুব সহজ। সভ্যতার আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানব সংস্কৃতির যেসব বিচিত্র বিকাশ ঘটেছে, আমরা আজ বিজ্ঞান, কলা, কারিগরী বিদ্যার যেসব অভাবনীয় উন্নতি চোখের সামনে দেখতে পাই, তা নিঃসন্দেহে আর্যদের সৃষ্টিশক্তিরই ফল। এ থেকে আমরা এ সিদ্ধান্তেই আসতে পারি যে একমাত্র আর্যরাই এক উন্নত ধরনের মুনষ্যত্ব বোধকে প্রতিষ্ঠিত করে। আমরা আজ প্রকৃত মানুষ বলতে যা বুঝি সে ধারণা তাদেরই সৃষ্টি। আর্যরা হচ্ছে সমগ্র মানবজাতির সেই প্রমিথিউস যার জ্বলন্ত জযুগল হতে আসে অলৌকিক প্রতিভার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। সেই সব অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জ্ঞান বিকাশের বিচিত্র অনেক রূপ ধরে সর্বব্যাপি অজ্ঞতার রহস্যময় অন্ধকার অপসারিত করে। এ আলোই মানুষকে প্রথম উন্নতির পথ দেখায় এবং পৃথিবীর অন্য সব প্রাণীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে সহায়তা করে। সেই আর্যরা যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে আবার সেই অজ্ঞতার গভীর অন্ধকার নেমে এসে পরিব্যপ্ত করে ফেলবে সমস্ত পৃথিবীতে। কয়েক হাজার বছরের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যাবে মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি। মরুভূমি হয়ে পড়বে সারা বিশ্ব।
সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠাতা, সংস্কৃতির ধারক ও বাহক এবং সংস্কৃতির ধ্বংসকর্তা— এ তিন শ্রেণীতে যদি সমগ্র মানবজাতিকে ভাগ করা হয় তাহলে আর্যরা অবশ্যই প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত হবে। এ আর্যরাই মানব সংস্কৃতির ভিত্তিভূমি রচনা করে। তার ওপরে তার প্রতিটি স্তম্ভ ও কাঠামো করে। শুধু বিশ্বের বিভিন্ন জাতি তাদের আপন আপন জাতীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারে সংস্কৃতির সেই কাঠামোতে রঙ ও রূপ দান করে। এ আর্যরাই মানবজাতীর উন্নত সৌধ রচনার উপযুক্ত পরিকল্পনা ও মাল মসলা সরবরাহ করে। বিভিন্ন জাতি তাদের আপন আপন মান অনুসারে এক একটা বিশেষ পদ্ধতিতে সেই উন্নতির সৌধ রচনা করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে কয়েক দশকের মধ্যে সমগ্র পূর্ব এশিয়ার অধিবাসীরা একটি সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ করে সেই সংস্কৃতিকে নিজেদের বলে অভিহিত করে। আসলে কিন্তু আমরা জানি এ সংস্কৃতির ভিত্তি গ্রীকদের রচিত এবং তা তাদের কলাকৌশলের সৃষ্টি। শুধু সেই সংস্কৃতিটির বহিরঙ্গটি অন্তত কিছু পরিমাণে এশিয়ার জাতিগুলোর নিজস্ব অর্থরেখার সৃষ্টি। অনেকে বলে থাকে যে জাপান তার নিজস্ব সংস্কৃতিকে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু বাস্তবে জাপান ইউরোপীয় সংস্কৃতি, জ্ঞানবিজ্ঞান ও তার প্রয়োগ পদ্ধতিকে পুরোপুরি গ্রহণ করে তার ওপর আপন জাতীয় বৈশিষ্ট্যের রঙ দিয়ে সেগুলোকে অলংকৃত করে। জাপানের জাতীয় জীবনের বহিরঙ্গটিতে তার নিজস্ব সংস্কৃতির কিছু নিদর্শন থাকলেও তার বর্তমান জাতীয় জীবনের আপন ভিত্তিটির সঙ্গে কিন্তু তার নিজস্ব দেশীয় সংস্কৃতির কোন সম্পর্ক নেই। জাপানের সমসাময়িক জীবন-ধারার বাস্তব রূপটি ইউরোপীয় ও আমেরিকান জ্ঞান বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির খাতেই বয়ে চলেছে। এ সংস্কৃতি হল মূলত আর্য সংস্কৃতি। এ সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞানের সুফলগুলোকে তাদের উন্নতির মূল ভিত্তি স্বরূপ গ্রহণ করার ফলেই প্রাচ্যের জাতি আধুনিক বিশ্বের অগ্রগতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে; ইউরোপ ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী বিদ্যার উজ্জ্বল কৃতিত্বগুলোকে ভিত্তি করেই প্রাচ্যের জাতিগুলোর দৈনন্দিন জীবন সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের জাতিগুলোর জীবন সংগ্রামের হাতিয়ার জোগায়। তবে সেই সব হাতিয়ারের বহিরঙ্গটি জাপানীদের জীবন যাত্রার সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে ধীরে ধীরে।
জাপানের ওপর এ আর্য সংস্কৃতির প্রভাব স্তব্ধ হয়ে যাবে যদি ইউরোপ আমেরিকা অকস্মাৎ ধ্বংস হয়ে যায়। তাতে জাপানের উন্নতির স্রোতটা মাত্র কয়েক দশক অব্যাহত থাকবে, পরে শুকিয়ে যাবে একেবারে। তাহলে জাপানের প্রাচীন স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যের প্রাধান্য লাভ করবে এবং বর্তমান সভ্যতা ও সংস্কৃতি সেই বিদ্যার জড়তার মধ্যে স্তরীভূত হয়ে পড়বে। আজ হতে কুড়ি বছর আগে যে দ্রিা থেকে একদিন অপসংস্কৃতির ডাকে তারা জেগে উঠেছিল। সুতরাং আমরা এ সিদ্ধান্তে যেতে পারি যে জাপানের বর্তমান। উন্নতির ধারাটা যেমন জনপ্রভাব থেকে উৎসারিত, তেমনি তার প্রাচীন সভ্যতার রূপচিত্ত বহিরাগত কোন প্রভাব হতেই উদ্ভূত হয়। একথা মনে করার যুক্তি এ যে প্রাচীন জাপানী সভ্যতার ধারাটা চলতে চলতে স্তব্ধ ও প্রস্তরীভূত হয়ে যায়। সভ্যতার এ অবক্ষয় ধরা হয় তখনই যখন কোন জাতি তার সৃষ্টিশীল সত্তা হারিয়ে ফেলে অথবা বহিরাগত যে প্রভাব একদিন জাতিকে জাগিয়ে তোলে, তার সংস্কৃতিকে উন্নতি ঘটায়, সেই প্রভাব সহসা প্রত্যাহত হয়। যদি দেখা যায় কোন দেশ তার সংস্কৃতির মূল উপাদান অন্য কোন বিদেশী সংস্কৃতি থেকে সগ্রহ করে এবং বাইরে থেকে সেই উপাদান আসার পথ বদ্ধ হয়ে গেলেই সেই জাতির সংস্কৃতির ধারাটা স্তব্ধ ও প্রস্তরীভূত হয়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে সে সংস্কৃতির সংরক্ষকমাত্র, সংস্কৃতির স্রষ্টা নয়।
এদিক দিয়ে আমরা যদি বিশ্বের বিভিন্ন জাতিকে বিচার করি তাহলে দেখতে পাব তাদের মধ্যে বেশির ভাগই মূল্যগতভাবে কোন সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে পারেনি। অন্য কোন দেশে সৃষ্ট কোন সংস্কৃতির ধারাটিকে গ্রহণ ও আত্মসাৎ করেছে মাত্র।
নিম্নে দৃষ্টান্ত থেকে ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারি।
আর্যজাতি সংখ্যায় স্বল্প হয়েও বিশ্বের বহু দেশ ও জাতিকে জয় করে এবং সেইসব বিজিত দেশের ভূমির উর্বরতা, জলবায়ুর ও কায়িক শ্রমের প্রাচুর্য প্রভৃতি এমন কতগুলো জীবনযাত্রাগত সুযোগ সুবিধা পায় যাতে তারা তাদের বুদ্ধি ও সংগঠন প্রতিভাকে আরো ভালভাবে বিকশিত করে তুলতে পারে। কয়েক শত বা কয়েক হাজার বছরের মধ্যে বিজেতারা বিজিত জাতির আদিম প্রাণহীন সংস্কৃতিকে প্রাণবন্ত করে তোলে। তবে এ নতুন সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে গিয়ে বিজিত জাতিরা তাদের দেশ ও জাতিগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে রূপটা কিছু পরিবর্তিত করে ফেলে। কিন্তু পরিশেষে দেখা যায় বিজেতারা তাদের জাতিগত রক্তকে অবিমিশ্র রাখার প্রাকৃতিক নিয়ম ও নীতি হতে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে এবং তারা বিজিত জাতিদের সঙ্গে তাদের রক্তগত সংমিশ্রণ ঘটাতে থাকে। এভাবে তাদের পৃথক সত্তাটি তার সব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে।
এক হাজার বছরের মধ্যেই দেখা যায় বিজিত জাতিগুলো বিজেতাদের রক্ত হতে তাদের ত্বকের যে যে অংশ উজ্জ্বলতা লাভ করেছিল, সে রঙ ও উজ্জ্বলতা ম্লান হয়ে গেছে অনেকখানি। বিজেতা জাতির যে জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও সত্তার দীপ্তি হতে বিজয়ী জাতি সংস্কৃতি ও জাতীয় উন্নতির মশালটি জ্বলে ওঠে, বিজেতা জাতির রক্ত ম্লান হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সেই আভার দীপ্তিও ম্লান হয়ে যায়। কিন্তু বিজেতাদের প্রভাব কালক্রমে ম্লান হয়ে গেলেও বিজেতাদের রক্তের মধ্যে বিজয়ীদের রক্তের রঙ কিছুটা রয়ে যায়। তাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উজ্জ্বলতায় একটা ক্ষীণ অংশ যা বিজেতাদের ওপর নেমে আসা সাংস্কৃতিক বিপর্যয় ও বর্বরতার অন্ধকারকে ঘন হতে দেয় না কিছুতে। যে অন্ধকার নতুন করে আচ্ছন্ন করে বিজিতদের, সেই অন্ধকারের মাঝে বিজয়ীদের জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অতীত উজ্জ্বলতার অংশটি কিরণ দিতে থাকে। সেই কিরণের আভায়। বর্তমানের কোন ভাবমূর্তি নয়, বিস্মিত অতীতের একটা দিক প্রতিফলিত হয়ে ওঠে শুধু।
তবে এমনও হতে পারে যে কালের বিবর্তনে ভবিষ্যতে কোন এক সময় বিজিত জাতি তাদের সংস্কৃতির সুপ্রাচীন স্রষ্টাদের সংস্পর্শে আবার আসতে পারে। তখন হয়ত তারা অতীত ঋণের কথা ভুলে যায়। তথাপি তাদের রক্তের মধ্যে বিজয়ীদের রক্তের যে একটা অংশ রয়ে যায়, সেই রক্তের প্রভাব তাদের প্রবৃত্তিকে আকর্ষণ করে নিয়ে যাবে বিজেতাদের দিকে। সুতরাং অতীতে যে জাতিগত সংমিশ্রণ বাধ্যবাধকতার মধ্য দিয়ে বয়ে ছিল, এবার তা হবে স্বচ্ছন্দে ও স্বেচ্ছায়। ফলে এক সাংস্কৃতিক উন্নতির ঢেউ নতুন করে প্রবাহিত হতে থাকবে এবং তা’ এ সংমিশ্রণের জন্য বিজেতা জাতির রক্ত নতুন করে দূষিত না হওয়া পর্যন্ত এভাবে সবকিছু চলতে থাকবে।
যারা বিশ্বের ইতিহাস ও গতিপ্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করতে চান তাদের এ দৃষ্টিকোণ থেকে কাজ করতে হবে।
সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে সব পরিবর্তন ঘটছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে সব জাতির নিজস্ব কোন সংস্কৃতি নেই, যারা বহিরাগত কোন সংস্কৃতির ধারক বা সংরক্ষক মাত্র তারা বিভিন্ন বিষয়ে উন্নতি করছে, আর আর্যদের মত যেসব জাতি এক উন্নত ধরনের স্রষ্টা ও প্রতিষ্ঠাতা তারা বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।
আমাদের জীবনে দেখা যায় প্রতিভাবান ব্যক্তি তাদের দেখে সাধারণত আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতই মনে হয়; কোন বিশেষ ঘটনা বা উপলক্ষ্য ছাড়া তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটে না। যখন জাতীয় জীবনে এমন কোন বিশেষ ঘটনা বা অবস্থার সৃষ্টি হয় যা দেখে সাধারণ মানুষ হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে, তখনি আপাত সাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তিরা তাদের প্রতিভার পরিচয় দেয়। এ কারণেই কোন জাতির জীবনে মাঝে মাঝে এতজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। যুদ্ধও এমন এক বিশেষ ঘটনা যার মাধ্যমে বুদ্ধিমান, শক্তিমান ও প্রতিভাবানরা তাদের অসাধারণত্বের পরিচয় দান করতে পারেন। কোন বিপর্যয়কালে দেখা যায় অনেক নিরীহ যুবক হঠাৎ সামনে এসে দৃঢ়সংকল্প ও স্থিরবুদ্ধির মাধ্যমে সেই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে তাদের আশ্চর্য প্রতিভা শক্তির পরিচয় দেয়। এ ধরনের কোন পরীক্ষামূলক ঘটনা ছাড়া কেউ বুঝতেই পারবে না কার মধ্যে এ আশ্চর্য এক বীরের শক্তি লুকিয়ে আছে। কোন প্রতিভা বা বীরত্বের সর্বসমক্ষে প্রকাশ ঘটাতে হলে বিশেষ কার্যপ্রেরণা ও প্রবৃত্তির দরকার। ভাগ্যের হাতুড়ীর যে নিষ্ঠুর আঘাত একজন সাধারণ মানুষকে সহজেই ভেঙে চুরমার করে দেয়, সে আঘাত কোন বীর বা প্রতিভাবান ব্যক্তির মাঝে এক ইস্পাতকঠিন প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়। প্রথমে প্রকৃত ঘটনার আঘাতে বীরদের ওপর থেকে সাধারণের খোলস খসে যায় আর তখন তাদের অন্তর্নিহিত অসাধারণ সত্তার কঠিনতম অংশটি বেরিয়ে পড়ে। তা দেখে সারা জগৎ বিস্মিত হয়ে যায়। জগতের লোকের ধারণা তাদের মতই এক আপাত সাধারণ লোকের মধ্যে এমন অসাধারণ গুণ ও শক্তি লুকিয়ে থাকতে পারে। যতবারই কোন প্রতিভার আবির্ভাব হয়, ততবারই এ নিয়মের পুনরাবৃত্তি ঘটে।
যে ব্যক্তি কোন সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী, জন্মের পর থেকে তার সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গটি ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির মত তার অন্তরের মধ্যে চাপা ছিল। যে কোন প্রতিভাই এমনি এক অন্তর্নিহিত সহজাত শক্তি। প্রতিভা কখনো কোন শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের সৃষ্টি নয়।
আমি আগেই বলেছি, আবার বলছি, এটা শুধু ব্যক্তির পক্ষে নয়, সমগ্র জাতির পক্ষেও প্রযোজ্য। যে সব জাতি বিভিন্ন সৃষ্টিশীল শক্তির পরিচয় দেয়, তারা জন্মগতভাবেই সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী। আপাত দৃষ্টিতে লোকে দেখতে না পেলেও তাদের স্বভাবের মধ্যেই সে শক্তি নিহিত থাকে। উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি যেমন কোন বিশেষ অবস্থা ছাড়া তার সহজাত প্রতিভার বিকাশ সাধন করতে পারে না, তেমনি কোন জাতিও উপযুক্ত কর্মপ্রেরণা বা অবস্থা ছাড়া তাদের সৃজনশীল প্রতিভাকে কার্যে রূপায়িত করতে পারে না।
এ সত্যের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হল সেই আর্যজাতি যারা আজও মানবজাতির সকল উন্নতি ও প্রগতির ধারক ও বাহক। ভাগ্য যখনি তাদের কোন বিশেষ অবস্থার ওপরে উপস্থাপিত করে, তখনি তাদের সহজাত শক্তি এক বিশেষ রূপে বিকাশ লাভ করে থাকে। এ সব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারা যেসব বিশিষ্ট সংস্কৃতি সৃষ্টি করে, সে সব সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট বিজিত দেশের ভূমি, প্রকৃতি, জলবায়ু ও অধিবাসীদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এর মধ্যে দেশের অধিবাসীদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কোন দেশের উন্নতি করতে গিয়ে যদি দেখা যায় সেখানে যন্ত্রপাতি ও কারিগরী বিদ্যার অভাব আছে, তাহলে সেখানে প্রচুর শ্রমশক্তির দরকার হয়। আর্যরা যদি তাদের বিজিত জাতিগুলোর যৌবনের শ্রমশক্তির সাহায্য না নিত, তাহলে পরবর্তীকালে তারা উন্নত ধরনের সংস্কৃতির সৃষ্টি করতে পারত না। যেমন প্রথমে অশ্ব ও বিভিন্ন পশুর সাহায্যে পরিবহন কার্য সম্পন্ন করার পর মানুষ যন্ত্রপাতি আবিস্কার করে।
উন্নত ধরনের সভ্যতার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অনুন্নত জাতিগুলো এক অত্যাবশ্যক উপাদান হিসেবে কাজ করে; তারা নিজেদের শ্রমশক্তির দ্বারা যন্ত্রের অভাব পূরণ করে। সভ্যতার প্রথম স্তরে পোষা পশুর পরিবর্তে বিজিত নিকৃষ্ট জাতির লোকদের বিভিন্ন কাজে লাগানো হত।
প্রথম প্রথম বিজিত লোকদের ক্রীতদাস হিসেবে যেসব কাজে লাগানো হত, পরে পোষণ মানানো পশুদের সেইসব কাজে লাগানো হয়। প্রথমে যেসব শক্রদের জয় করা হত তাদের লাঙল টানার কাজে নিযুক্ত করা হত, পরে এ কাজে বলদ ও ঘোড়াদের লাগানো হয়। একমাত্র অপদার্থ শান্তিবাদীরাই এটাকে মানবজাতির অধঃপতন বলে অভিহিত করতে পারে। আজকের মানুষের সভ্যতার যে উন্নতি হয়েছে সেখানে ওঠার জন্য এ ধরনের বিবর্তনের প্রয়োজন ছিল।
অসংখ্যা ক্রম বিবর্তন ও ক্রম পর্যায় সমন্বিত মানবজাতির উন্নতি বা অগ্রগতির ব্যাপারটাকে একটা খণ্ডহীন মইয়ের ওপরে ওঠার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। একটি মইয়ের মধ্যে অনেক অংশ বা সিঁড়ি আছে। কিন্তু নিচের অংশটি অতিক্রম না করে কেউ উজ্জ্বলতার অংশটায় উঠতে পারে না। আর্যরা তখন তাদের বাস্তবতা চোখের বশবর্তী হয়ে যেসব গ্রহণযোগ্য মনে করেছিল সেই সবই গ্রহণ করেছিল; আধুনিক শান্তিবাদীদের কথা মত চলেনি। তবে এ বাস্তব নির্ণয় করা ও সেই মতে চলা খুবই কঠিন। একমাত্র এ পথই মানুষকে নিয়ে যেতে পারে তার আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে।
কিন্তু এমন অনেক লোক আছে যারা মানুষকে শুধু স্বপ্নের রাজ্যে নিয়ে যায়। এ সব স্বপ্নদর্শীরা মানুষকে তাদের প্রকৃত লক্ষ্য থেকে দূরে সরিয়ে নেয়।
সুতরাং দেখা যায় আর্যরা কোন নিকৃষ্ট অনুন্নত জাতির সংস্পর্শে আসামাত্র সভ্যতার প্রথম স্তরটি গড়ে ওঠে। এ স্তর গড়ে ওঠে তখনি যখন সেই অনুন্নত জাতির লোকেরা ক্রমবর্ধমান মানব সভ্যতার এক যান্ত্রিক উপাদান হিসেবে কাজ করতে থাকে।
এভাবে আর্যরা এক সুনির্দিষ্ট পথের সন্ধান পায়। বিজেতা হিসেবে তারা নিকৃষ্ট অনুন্নত জাতিগুলোকে জয় করে তাদের নেতৃতাধীনে তাদের কর্মশক্তিকে এক সুসংগঠিত পদ্ধতিতে গঠন করতে থাকে। পরাজিতরা বিজয়ীদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য অনুসারে চলতে বাধ্য হয়। কিন্তু পরাজিতদের ওপর আর্যরা তাদের ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য জোর করে চাপিয়ে দিলেও এর ফলে তাদের স্বার্থ প্রথমে রক্ষা পায়নি। আগের যুগের থেকে তাদের জীবনযাত্রা আরো সহজ হয়ে উঠেছিল। তারা শুধু বিজয়ী হিসেবে বিজেতাদের প্রভূতুই রক্ষা করে চলেনি, তারা তাদের মাঝে সভ্যতারও বিস্তার করেছিল। এটা আর্যদের সহজাত কর্মক্ষমতা, যোগ্যতা, প্রতিভা ও জাতিগত রক্তের সংরক্ষণ থেকে সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু যখনি বিজিতরা বিজেতাদের স্তরে ধীরে ধীরে তাদের ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে পৌঁছে যায়, তখনি এতদিন ধরে বিজেতা ও বিজিতদের মধ্যে যে বাধা ও ব্যবধান বিরাজ করেছিল তা’ সব অবলুপ্ত হয়ে যায়। আর্যরা তাদের জাতীয় সত্তা ও রক্তের পবিত্রতাকে অক্ষুণ্ণ ও অমিশ্রিত করে রাখতে না পারায় তাদের নিজেদের হাতে গড়া স্বর্গ বিজেতাদের কাছেই হারিয়ে ফেলে। এভাবে তারা জাতিগত সংমিশ্রণের মধ্যে ডুব দিয়ে তাদের সাংস্কৃতিক সৃষ্টিশীলতাকে বাড়িয়ে ফেলে। তারা তাদের উত্তর পুরুষের বংশধারা হতে বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে দেহ ও মনের দিক থেকে তাদের দ্বারা আদিম অধিবাসীদের মত হয়ে ওঠে, তারা অবশ্য কোনরকমে তাদের দ্বারা নির্মিত সৌধটিকে টিকিয়ে রাখে। কিন্তু তাদের সেই মূল সংস্কৃতির প্রাণসত্ত্বাটা প্রস্তরীভূত হয়ে যেতে থাকে ধীরে ধীরে এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত প্রাণশক্তির সকল গৌরব বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে যেতে থাকে; এভাবেই সমস্ত সংস্কৃতি ও সাম্রাজ্যের ধ্বংস নেমে আসে। রক্তগত সংমিশ্রণজনিত জাতীয় অধঃপতনই প্রাচীন সভ্যতাগুলোর পতনের প্রধানতম কারণ। যুদ্ধে দ্বারা কখনো কোন জাতি ধ্বংস হয় না। সম্পূর্ণরূপে জাতিগত রক্তের অমিশ্রিতা ও শুচিতা হতে যে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে ওঠে, সেই প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলায় ধ্বংস ও অধঃপত ঘটে প্রাচীন আর্যদের। যুদ্ধ, বড় ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো জাতিগত অবক্ষয় প্রবৃত্তির এক বাস্তব প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।
আর্যদের প্রভুত্বের কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যাবে আর্যদের মধ্যে আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি শুধু প্রধান নয়, তাদের প্রবৃত্তির প্রকাশের রীতিনীতিটিও বড় অদ্ভূত। আত্মগত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে দেখা যায় বাচার প্রবৃত্তি সকল প্রাণীর মধ্যেই সমান— শুধু তার প্রকাশের পদ্ধতিটি ক্ষেত্রবিশেষে আলাদা। আদিম প্রবৃত্তিগুলির অন্যতম আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি মানুষের ব্যক্তিগত অহংবোধের বাইরে কোন কাজ করতে পারে না। আমরা এ প্রবৃত্তিকেই অহংবোধ নাম দিয়েছি। এ অহংবোধের মধ্যেই মানুষের সমস্ত কালচেতনাও সীমাবদ্ধ। এ কালচেতনার অর্থ হল এ যে বর্তমানকালই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানুষের জীবনে। অহংভিত্তিক এ কালচেতনার মধ্যে ভবিষ্যতের কোন স্থান নেই। সকল জীব শুধু নিজের জন্য বাঁচে, তারা একমাত্র যখন ক্ষুধা অনুভব করে তখনি খাদ্যের অনুসন্ধান করে। একমাত্র আত্মরক্ষার কারণ ছাড়া তারা যুদ্ধ করে না। যতদিন এ আত্মরক্ষণ প্রবৃত্তি মানুষের মনে প্রবল থাকে ততদিন কোন জনসমাজ বা সম্প্রদায় গড়ে উঠতে পারে না। এমন কি এ অবস্থায় কোন পরিবারও গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। কারণ নরনারীর যে সম্পর্ক কোন পরিবারকে গড়ে তোলে সেই সম্পর্কের ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিটা ব্যক্তিগত সীমানা পার হয়ে যায় আর একটি জীবন পর্যন্ত প্রসারিত হয়। অর্থাৎ মানুষ সবসময় নিজের সঙ্গে তার জীবনের সাথীর জীবনকেও রক্ষা করে চলার চেষ্টা করে। পুরুষ নারীর জন্য খাদ্যসংগ্রহ করে এবং নারী পুরুষ উভয়ে মিলে তাদের সন্তানদের আহারের ব্যবস্থা করে থাকে। তারা সব সময় একে অন্যকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হয়। এভাবে আমরা সংকীর্ণ পথে হলেও এক একটি পরিবারের মধ্যে মানুষের আত্মত্যাগের প্রথম পরিচয় পাই। এ প্রবৃত্তি যখন পরিবারের সীমানা অতিক্রম করে সমাজ সম্পর্কের বৃহত্তর ক্ষেত্রের মধ্যে প্রসারিত হয়, তখনই রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্ভবপর হয়ে ওঠে।
মানব জাতির মধ্যে যারা নিকৃষ্ট শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত তারা তাদের পরিবারের বাইরে আত্মত্যাগের প্রবৃত্তির পরিচয় দিতে পারে না। ব্যক্তিস্বার্থকে পেছনে সরিয়ে কারোর জন্য কিছু করার ও আত্মত্যাগের প্রবৃত্তিটির যত বেশি সম্প্রসারণ ঘটে ততই বড় বড় সমাজ ও সম্প্রদায় গড়ে ওঠে।
পরের জন্য ব্যক্তিগত কাজকর্ম, কামনা বাসনা ও প্রয়োজন হলে নিজের জীবন পর্যন্ত ত্যাগ করার নীতি আর্যদের মধ্যেই পুর্নমাত্রায় বিকাশ লাভ করে। আর্যদের মহত্বের ভিত্তিভূমিটি কোন বুদ্ধিগত উর্ষকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠেনি। সমাজের স্বার্থেই আপন আপন বুদ্ধিগত শক্তি ও উৎকর্ষকে ত্যাগ করার সুমহান বাসনাই হল সেই মহত্বের ভিত্তি। এখানে দেখা যায় আত্মরক্ষার প্রবৃত্তিটি এক মহত্তম রূপ পরিগ্রহ করেছে। কারণ আর্যরা স্বেচ্ছায় সমাজের সুখ ও স্বার্থের কাছে তাদের ব্যক্তিগত অহংবোধকে বিলিয়ে দেয় এবং প্রয়োজনবোধে নিজের জীবন পর্যন্ত বিসর্জন দেয়।
আর্যদের সংগঠন ক্ষমতা এবং বিশেষ করে কোন সংস্কৃতিকে গড়ে তোলায় তাদের আশ্চর্য ক্ষমতার মূল উৎসটি একান্তভাবে বুদ্ধিগত নয়। তা যদি হত তাহলে তাদের বুদ্ধিগত শক্তি ও উৎকর্ষ ধ্বংসাত্মকও হতে পারত, তাহলে তারা এতখানি সাংগঠনিক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারত না। কারণ সমাজের বৃহত্তর স্বার্থ ও সেবায় ব্যক্তিগত স্বার্থ ও মতামত বিসর্জন দেবার অকুণ্ঠ প্রস্তুতি ও প্রবৃত্তির ওপরেই নির্ভর করে মানুষের সকল সাংগঠনিক ক্ষমতার সার্থকতা। সমাজের উন্নতি ও সেবায় আত্মনিয়োগ করার প্রশিক্ষণ সে পায়। এক্ষেত্রে সে প্রত্যক্ষভাবে নিজের জন্য বা ব্যক্তিগত স্বার্থ পূরণের জন্য কাজ করে না। তাদের সকল উৎপাদক কর্মশক্তি সমাজের সকল মানুষের কর্মের একটি অংশ বলে মনে করে। সে নিজেকেই এ সাজের এক অংশ হিসেবে ধরে নেয়। কম’ শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ–নিজের উপার্জনের জন্য কোন কাজ করা নয়, এ শব্দের অর্থ হল এমন কিছু করা যাতে ব্যক্তিগত স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের স্বার্থও পূরণ হবে। যখন কোন মানুষের কোন কর্ম একান্তভাবে আত্মরক্ষণ ও ব্যক্তিগত স্বার্থ পুরণের জন্য পরিচালিত হয়, তখন তার সে কাজকে চৌর্যবৃত্তি বলে।
সমাজের স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলার এ নীতি ও প্রবৃত্তিই প্রকৃত মানব সভ্যতার প্রধানতম ভিত্তি। এ নীতি ও প্রবৃত্তির ফলে বিশ্বের এমন অনেক অক্ষয় কীর্তি গড়ে উঠেছে যার জন্য তার স্রষ্টারা জীবিতকালে কোন প্রতিদান বা প্রতিফল লাভ করে যেতে পারেনি; তাদের মৃত্যুর পর তাদের বংশধরেরা সেইসব কীর্তির সুফল ভোগ করে। এ নীতি ও প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়েই মানুষ এমন অনেক কাজ করে যার জন্য সৎ ও দীনহীন জীবিকা ছাড়া প্রতিদানে কিছুই সে পায় না। কিন্তু এ সৎ জীবিকাই সমাজের ভিত্তিভূমিকে দৃঢ় করে তোলে। কোন কৃষক, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কর্তা বা সরকারি কর্মচারী যিনিই হোন না কেন— যখন কোন ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত সুখ সমৃদ্ধির কথা চিন্তা না করে সমগ্র সমাজের বা মানবজাতির জন্য কাজ করে তখন তারাই এক সুমহান নিঃস্বার্থ কর্মপ্রবৃত্তির মূর্ত প্রতীক। অনেক সময় মানুষ তার এ প্রবৃত্তিও কর্মতৎপরতার তাৎপর্য না জেনেই তার পরিচয় দিয়ে থাকে।
খাদ্যসংগ্রহ, মানবজাতির উন্নতির প্রাথমিক ভিত্তি রচনা বা মানব সভ্যতা সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ প্রভৃতি যে কোন কাজের ক্ষেত্রে মানুষ নিঃস্বার্থভাবে যা কিছু করে তাতেই তার ত্যাগের পরিচয় পাওয়া যায়। সমাজের স্বার্থে প্রাণ বিসর্জনই হল এ ত্যাগের সুমহান প্রবৃত্তির সর্বশ্রেষ্ঠ বাস্তবরূপ। একমাত্র এ ত্যাগের মাধ্যমেই মানুষ যুগ যুগ ধরে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির অধিকারী হয়েছে, সে সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে সে রক্ষা করে যেতে পারবে। এভাবে কাজ করে গেলে মানুষের সভ্যতাকে প্রকৃতি বা মানুষ কেউ কখনো ধ্বংস করতে পারবে না।
জার্মান ভাষায় একটি শব্দ আছে যার অর্থ হল ব্যক্তিস্বার্থ থেকে সমাজের সর্বসাধারণের স্বার্থ সবসময় বড়। যে মৌন প্রবৃত্তি থেকে এ ধরনের কর্মের উদ্ভব হয়, অহং ও আদর্শের পার্থক্যই সেই প্রবৃত্তির উৎস। এর অর্থ সমাজের স্বার্থে যে কোন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকার এক স্বীকৃত বাসনা।
এ বিষয়ে একটি কথা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সেটি হল এ যে আশীবাদের অর্থ ভাবানুরাগের উচ্ছসিত প্রকাশ নয়, আদর্শবাদের প্রকৃত অর্থ হল মানব সভ্যতার জন্য অত্যাবশ্যক এক ভিত্তি। এ আশীর্বাদ হতেই মানবিক’ শব্দটির উৎপত্তি। এ মনোভাবের জন্য সারা বিশ্বে আর্যদের এত প্রতিষ্ঠা। মানবজাতি এ ধারণাটির জন্য সারা বিশ্ব আর্যদের নিকট ঋণী। মানবতার এ আদর্শ থেকে এমন একটি সৃষ্টিশীল শক্তির উদ্ভব হয় যে শক্তির সাহায্যে মানুষ তার দেহগত শক্তির সঙ্গে বুদ্ধিগত শক্তির মিলন ঘটিয়ে মানব সভ্যতার সৌধটিকে গড়ে তোলে।
এ আদর্শবাদ ছাড়া মানুষের সকল বুদ্ধিবৃত্তি সৃষ্টি শক্তিহীন বন্ধ্যা বাইরের ঘটনায় পর্যবসিত হবে এবং ঘটনার কোন বিশেষ মূল্য বা বৃহত্তর কোন তাৎপর্য থাকবে না।
প্রকৃত আদর্শবাদের অর্থই হল ব্যক্তি স্বার্থকে সমষ্টি স্বার্থের অধীনস্থ করে তোলা। তাই সমাজের বৃহত্তর স্বার্থপূরণের আদর্শ প্রকৃতির চূড়ান্ত উদ্দেশ্য পূরণের পথে নিয়ে যায় মানুষকে।
যে আদর্শবাদ যত বিশুদ্ধ, তা তত গভীর জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত। একটি বালককে ভাববাদী শান্তিবাদীরা যতই বোঝাক না কেন, সে তাদের কথা ভালোভাবে না বুঝলে প্রত্যাখ্যান করবে এবং তার জাতির আদর্শের খ্যাতিরে প্রাণ বিসর্জন দেবে।
কোন কিছু না বুঝলেও বালকটি অন্তত এ কথাটা বেশ বোঝে যে প্রয়োজন হলে কোন ব্যক্তিজীবনের বিনিময়ে একটি প্রজাতিকে বাঁচাতে হবে। সে তাই ভাববাদী শান্তিবাদের নীতিকথার প্রতিবাদ করবে। যে স্বার্থবাদীরা এক একজন ছদ্মবেশী ব্যর্থতান্ত্রিক অহংবেশী কাপুরুষকে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরোধিতা করে চলেছে। মানবসভ্যতার বিবর্তনের জন্য যা অত্যাবশ্যক তাহল এ যে সমাজের স্বার্থে আত্মত্যাগের আদর্শে একটি ব্যক্তি উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। এ আদর্শকে ত্যাগ করে কোন মানুষ কখনই সেই ভণ্ডদের কথা শুনবে না বা তাদের দ্বারা প্রভাবিত হবে না যারা প্রকৃতির থেকে বেশি জানার ভান করে এবং যারা ধৃষ্টতাবশত প্রকৃতির বিধানের সমালোচনা করে।
একমাত্র যখন এ আদর্শ লুপ্ত হয়ে যেতে বসে, তখনি সেই শক্তির মধ্যে আমরা একটি চিত্র দেখতে পাই যে শক্তি ছাড়া কোন সভ্যতাই টিকে থাকতে পারে না। যে মুহূর্তে মানুষের স্বার্থপরতা ও অহংবোধ সমাজে প্রাধান্য লাভ করে, সেই মুহূর্তে সমাজ সম্পর্কের বন্ধনটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তখন মানুষ সমাজকে বাদ দিয়ে আত্মসুখের সন্ধান করতে গিয়ে স্বর্গ থেকে নরকে পতিত হয়।
যারা সারাজীবন সুখের সন্ধান করে যায়, ভবিষ্যত বংশধরেরা তাদের মনে রাখে না। তারা মনে রাখে তাদেরই কথা, সেইসব বীরদের কথা, যারা তাদের ব্যক্তিগত সুখ জলাঞ্জলী দিয়েছিল।
ইহুদিরা জাতি হিসেবে আর্যদের সম্পূর্ণ বিপরীত। সারা পৃথিবীতে আর এমন একটি জাতিও নেই যাদের মধ্যে আত্মসংরক্ষণের প্রবৃত্তিটি এতখানি প্রবল। যারা মনে করে তারা ঈশ্বরপ্রেরিত জাতি। পৃথিবীতে এমন কোন জাতি আছে হাজার বছরের মধ্যেও যে জাতির চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়নি। আর কোন জাতি সর্বাত্মকভাবে বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছে? কিন্তু এত বিরাট পরিবর্তন সত্ত্বেও ইহুদি জাতি যেখানে ছিল সেখানেই আছে, তাদের মনপ্রাণের কোন পরিবর্তনই হয়নি। তাদের জাতিগত সংরক্ষণ ও বাঁচার প্রবৃত্তি এমনই দুর্মর।
ইহুদিদের বুদ্ধিগত কাঠামোটা হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে উঠেছে। আজকাল লোকে ইহুদিদের ধূর্ত বলে। অবশ্য একদিক দিয়ে ইহুদিরা বহু যুগ থেকে তাদের ধূর্তামীর পরিচয় দিয়ে আসছে। তাদের বুদ্ধিগত শক্তি ও চাতুর্যের কাঠামোটি তাদের কোন অন্তর্নিহিত বিবর্তনের ফল নয়, যুগে যুগে বাহিরের অভিজ্ঞতা ও ঘটনা থেকে যে বাস্তব শিক্ষা লাভ করেছে, তার উপাদানেই গড়ে উঠেছে তাদের বুদ্ধিগত কাঠামোটি। মানুষের মন বা আত্মা পর পর ক্রমপর্যায়ের স্তরগুলো পার না হয়ে কখনো ওপরে উঠতে পারে না। ওপরের যে কোন স্তরে উঠতে হলে আগে তার নিচের স্তরটি অতিক্রম করতে হবে। যে কোন সভ্যতার ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থে অতীতের একটি জ্ঞান আছে। মানুষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেই তার সকল চিন্তাভাবনার উদ্ভব হয়। যুগ যুগ ধরে সখি পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতা থেকেই মানুষের বেশি চিন্তা ভাবনা গড়ে ওঠে। সভ্যতার সাধারণ স্তরের কাজ হল প্রতিটি মানুষকে এমন এক প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করা, যার ওপর ভিত্তি করে সে সকলের সঙ্গে জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির মান এগিয়ে নিয়ে চলতে পারে। যারা আজকের যুগের অগ্রগতিকে বুঝতে চায় ও সেই অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখতে চায়, তাদের কাছে এসব জীবন-জিজ্ঞাসা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের কোন প্রতিভাসম্পন্ন মহাপুরুষ বা মনীষী সহসা তার কবর থেকে যদি উঠে আসেন, তিনি এ যুগের অগ্রগতির কথা কিছুই বুঝতে পারবেন না। অতীতের কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে এ যুগে এসে এ যুগের গতিপ্রকৃতি বুঝতে হলে তাকে অনেক প্রাথমিক জ্ঞান সঞ্চয় করতে হবে, যে জ্ঞান আজকের যুগে ছেলেরা আপনা থেকে খুব সহজ ভাবে পেয়ে যায়।
ইহুদি জাতির নিজস্ব কোন সভ্যতা ছিল না। কেন ছিল না তা আমি পরে বলব। যেসব সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব বিভিন্ন দেশ চোখে দেখেছে বা হাতের কাছে পেয়ে গেছে–সেই সব কৃতিত্বের দ্বারাই তাদের এ বুদ্ধিবৃত্তিকে উন্নত করেছে।
এর উল্টো ঘটনা কখনো দেখা যায়নি।
যদিও ইহুদিদের আত্মোন্নতির প্রকৃতি অন্যান্য জাতির থেকে আরো প্রবল এবং তাদের বুদ্ধিবৃত্তি অন্যান্য জাতির থেকে কিছুমাত্র কম নয়, তথাপি একটা দিক দিয়ে বড় রকমের একটা অভাব দেখা যায় তাদের জাতীয় চরিত্রে। সাংস্কৃতির উন্নতির জন্য যে জিনিসটার সবচেয়ে বেশি দরকার সেই আদর্শবোধ তাদের একেবারেই নেই। ইহুদিদের মধ্যে দেখা যায় তাদের আত্মত্যাগের প্রবৃত্তিটি আত্মসংরক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার উর্ধ্বে উঠতে পারে না তারা কখনো। তাদের মধ্যে যে জাতীয় সংহতি দেখা যায় তা আদিম সঙ্গপ্রবণতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা উল্লেখযোগ্য যে, যতদিন কোন বিপর্যয় তাদের জাতীয় অস্তিত্বকে বিপন্ন করে দেবার ভয় দেখায়, ততদিনই তারা পারস্পরিক নিরাপত্তার জন্য ঐক্যবদ্ধ ও সংহত থাকে। এ জাতীয় বিপর্যয়ই তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাবকে অপরিহার্য করে তোলে। একদল নেকড়ে যেমন একযোগে তাদের শিকারের বস্তুকে আক্রমণ করার পর তাদের ক্ষুধা মিটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দল থেকে পৃথক হয়ে পড়ে, তেমনি ইহুদিরাও ঠিক তাই করে।
ব্যক্তিগত আত্মরক্ষার জন্য যেটুকু দরকার সেইটুকু ত্যাগ করতেই তারা প্রস্তুত সব সময়। তার বেশি নয়। ইহুদিরা একমাত্র তখনই ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে যখন কোন সাধারণ এক বিপদ তাদের সামনে এসে দাঁড়ায় অথবা কোন সাধারণ শিকারের বস্তু তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কিন্তু যখন সেই বিপদ কেটে গিয়ে শিকারের বন্ধু হাতের মুঠোয় এসে পড়ে, তখন তাদের আপাতদৃষ্ট সাময়িক সংহতি বোধ উবে যায় মুহূর্তে। তখন দেখা যায় যে জাতি একদিন ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করেছে আজ তারাই পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদে মত্ত হয়ে উঠেছে।
ইহুদিরা ছাড়া পৃথিবীতে যদি অন্য কোন জাতি না থাকত তাহলে তারা নিজেরা মারামারি করে একে অন্যকে ধ্বংস করে ফেলত; অবশ্য যদি হঠাৎ কোন আত্মত্যাগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও দীক্ষিত হয়ে সব ঝগড়া মারামারি নিজেরা বন্ধ করে ফেলত তাহলে সে কথা স্বতন্ত্র। সুতরাং কেউ যদি ইহুদিদের পারস্পরিক সহযোগিতার সাময়িক নীতিটাকে আত্মত্যাগের আদর্শ বলে মনে করে বা ব্যাখ্যা করে তাহলে সে ভুল করবে।
তারা যা কিছু করে ব্যক্তিগত অহংবোধের দ্বারা প্রণোদিত হয়েই করে। আর এ জন্যই দেখা যায় ইহুদিদের রাষ্ট্রের কোন নির্দিষ্ট ভৌম সীমানা নেই। যে রাষ্ট্রের কোন ভৌম সীমানা নেই, সে রাষ্ট্র কখনো প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। যদি না সে রাষ্ট্রের নাগরিকদের সকল মর্মপ্রেরণা ও কর্ম প্রবণতা কোন ত্যাগের আদর্শের দ্বারা পরিচালিত হয়। এ আদর্শ যে জাতির নেই সে জাতির সভ্যতাও তার ভিত্তিভূমি হারিয়ে ফেলে।
এ কারণে ইহুদিদের বুদ্ধিবৃত্তি যথেষ্ট থাকলেও তাদের নিজস্ব কোন সংস্কৃতি নেই। ইহুদি জাতির মধ্যে আজ যে সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়, সে সংস্কৃতি তাদের নিজস্ব সৃষ্টি নয়, তা অন্য সব জাতির দান। শুধু তাই নয়, তাদের হাতে পড়ে সেই সংস্কৃতির মানের অধোগতি ঘটেছে।
মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে ইহুদিদের স্থান কোথায় এ বিষয়ে যদি আমরা আলোচনা করতে যাই, তাহলে আমাদের একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে শিল্পের ক্ষেত্রে ইহুদিদের কোন নিজস্ব সৃষ্টি নেই। স্থাপত্য ও সঙ্গীতবিদ্যা কলাবিদ্যার এ দু’টি প্রধান ক্ষেত্রে ইহুদিদের কোন মৌলিক সৃষ্টিশীল প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না। শিল্পের ক্ষেত্রে যখনি তারা কিছু সৃষ্টি করতে আসে তখনি তারা অন্য জাতির কোন না কোন শিল্পরীতিকেই ভিন্ন উপায়ে তৈরি করার চেষ্টা করে। যেসব জাতি সভ্যতার স্রষ্টা ও প্রবর্তক, যারা সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী, তাদের যেসব গুণ আছে ইহুদি জাতির তা নেই।
কি পরিমাণে ইহুদিরা অপর জাতির সভ্যতাকে আত্মসাৎ করতে পেরেছে বা তার অবনতি ঘটিয়েছে তা বোঝা যাবে একটা বিষয়ে। তারা বানরদের মত শুধু অনুকরণ প্রবৃত্তিরই পরিচয় দিয়ে থাকে। যে গতিশীল সৃষ্টিশীলতা কোন মহৎ নাট্যসৃষ্টির জন্য একান্তভাবে আবশ্যক তা তাদের নেই। ওপরে যে যত কলাকৌশলই দেখাক না কেন, তাদের সৃষ্ট শিল্পবস্তুর কোন প্রাণ নেই। অথচ তাদের সংবাদপত্রগুলো তাদের এ অপূর্ণতাকে ঢাকার জন্য এগিয়ে আসে। এ অপূর্ণতা ঢাকা দেবার জন্য এক মিথ্যা সাফল্যের জয়ঢাক পেটায়। তখন পৃথিবীর সবাই মনে করে যে শিল্পীর এত প্রচার তার মধ্যে নিশ্চয় কোন বস্তু আছে। অথচ আসলে সে শিল্পী কুশলী নকল-নবীশমাত্র।
যে সৃষ্টিশীল শক্তি কোন সভ্যতার প্রবর্তন বা মানব জাতির উন্নতির জন্য অত্যাবশ্যক ইহুদিদের তা নেই। ইহুদিদের কোন আদর্শ না থাকায় তারা সৃজনাত্মক কোন কাজে নিযুক্ত না হয়ে ধ্বংসাত্মক খাতেই প্রবাহিত হয়ে থাকে।
ইহুদিদের কখনো কোন স্থায়ী রাষ্ট্র ছিল না বলেই তাদের কোন নিজস্ব সভ্যতা গড়ে ওঠেনি। অথচ ইহুদিরা আবার ঠিক যাযাবরও নয়। যাযাবরেরা এক-এক সময়ে এক এক জায়গায় বাস করে, যদিও সে জায়গা কোন ভৌম সীমানা দিয়ে ঘেরা যাবে না। তারা সে জায়গায় চাষ আবাদ করে না। তার স্বপক্ষে তাদের যুক্তি এ যে ভূমি উর্বর না হওয়ায় প্রতি বছর সমান ফসল ফলান যেতে পারে এমন কোন কথা নেই। এক নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসলের নিশ্চয়তা না থাকলে কোন মানুষের পক্ষে এমন কোন জায়গায় বসবাস করা সম্ভব নয়। আর্যরাও প্রথমে যাযাবর জীবন-যাপন করত। আমরা জানি আমেরিকায় উপনিবেশিক যুগের প্রথম যুগে মানুষ শিকারের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করত। পরে তারা আরো শক্তিবৃদ্ধি করে বনজঙ্গল পরিষ্কার করে আদিম অধিবাসীদের তাড়িয়ে দেয়। এভাবে ধীরে ধীরে তারা সারা দেশ জুড়ে বসতি স্থাপন করে।
কিন্তু আর্যরা প্রথমে যাযাবর জীবনযাত্রা করলেও তারা ইহুদিদের মত ছিল না। ইহুদিরা কোনদিন ঠিক যাযাবর ছিল না।
ইহুদীরা যাযাবর নয়, তারা পরগাছা বা পরজীবি। তারা একটির পর একটি রাজ্য ত্যাগ করে একস্থান থেকে অন্যস্থানে গেছে; তার কারণ এটা নয় যে কোন এক নীতির বশবর্তী হয়ে গেছে। স্বেচ্ছায় তারা স্থান ত্যাগ করেছে। স্থানীয় অধিবাসীদের চাপে পড়েই সেইস্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে তারা।
ইহুদিরা কখনো কোনদিন যাযাবর ছিল না, কারণ তারা যে জায়গা দখল করতে পারত, সে জায়গা ছাড়ার কথা মনেও ভাবত না। ক্রমে একটু সুযোগ পেলেই আশেপাশের জায়গা দখল করে ফেলত। তখন তাদের সে জায়গা থেকে বিতাড়িত করা অন্য জাতির পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে। তারা এমন এক দুষ্ট জাতি যারা তাদের আশ্রয় দেয় তাদের অবিলম্বে মেরে ফেলে।
এভাবে দেখা যায় ইহুদিরা সব সময় পরের রাজ্যে বাস করে এসেছে এবং আশেপাশের আরো কিছু রাজ্য দখল করে নিয়েছে। কিন্তু এ সব রাজ্যগুলোর মধ্যে তারা ধর্মসম্প্রদায়ের মুখোস পরিয়ে তাদের একটা নিজস্ব রাষ্ট্র গড়ে তুলত। যখন তারা উপযুক্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন তারা সে মুখোস খুলে ফেলে আপন স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করত, তাদের এ রূপ দেখতে কেউ চায়নি।
যে জীবন ইহুদিরা যাপন করত সে জীবন হল পরগাছার জীবন। এ জন্য এক বিরাট মিথ্যার ওপরে গড়ে উঠেছিল ইহুদিদের জীবন। দার্শনিক শোপেন হাওয়ারের মতে ইহুদিরা বিরাট মিথ্যাবাদী।
তারা অন্যান্য জাতি ও রাষ্ট্রের মধ্যে বাস করতে পারত যতদিন তারা এ কথা বলে ভুল বুঝিয়ে রাখতে পারত যে তারা কোন পৃথক জাতি নয়, তারা এক বিশেষ ধর্মমতের প্রতিনিধিমাত্র।
যাতে অন্যের মধ্যে পরগাছা হয়ে থাকতে পারে সেজন্য ইহুদিরা নিজেদের স্বরূপ প্রকাশ করত না। তারা জানত ব্যক্তিগতভাবে তারা যত বুদ্ধিমান হয়ে উঠবে ততই তারা অপরকে ঠকাতে পারবে। তারা এতদূর মানুষকে প্রতারিত করতে সফল হত যে তারা যে জাতির আশ্রয়ে থাকত তাদের এ ধারণা হত যে ইহুদিরা ফরাসী হতে পারে, আবার ইংরেজও হতে পারে। ওদের জাতিভেদ বলে কোন জিনিস নেই। ওদের সঙ্গে তাদের একমাত্র অর্থ ছাড়া অন্য বিষয়ে কোন সার্থকতাই নেই। যে সমস্ত রাষ্ট্রের প্রশাসন যন্ত্রে কার্যরত লোকদের কোন ঐতিহাসিক কাল নেই, ইহুদিরা হল সেই জাতের। ব্যাভেরিয়ার সরকারের অনেক কর্মচারী জানে না যে ইহুদিরা এক স্বতন্ত্র জাতি, তারা শুধু এক বিশেষ ধর্মমতের প্রতিনিধি মাত্র। কিন্তু ইহুদিদের পত্র-পত্রিকাগুলি একথা মানতেই চায় না। বহু প্রাচীনকালে ইহুদিরা সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ করতে গিয়ে এমন সব উপায়ের আবিষ্কার করে যার দ্বারা তারা যেখানে থাকে সেখানকার মানুষের কাছে থেকে সহানুভূতিটুকু লাভ করে।
কিন্তু ধৈর্যের ক্ষেত্রেও ইহুদিরা পরের অনুকরণ করেছে। তাদের ধর্ম ও সাংস্কৃতিক সকল ক্ষেত্র জুড়ে প্রসারিত হয়। ইহুদিদের চেতনা ও অনুভূতি হতে স্বতস্ফুর্তভাবে উদ্ভূত কোন ধর্ম বিশ্বাস গড়ে ওঠেনি। এ পার্থিব জীবন ও জগতের বাইরে এক মহাজীবনে বিশ্বাস একেবারে অপরিচিত তাদের কাছে। আর্যদের মতে মৃত্যুত্তীর্ণ এক মহাজীবনের প্রতি বিশ্বাস ছাড়া কোন ধর্মমতের বন্দনা সম্ভব নয়। ইহুদিদের ধর্মশাস্ত্রে এ মৃত্যুত্তীর্ণ মহাজীবনের কোন কথা লেখা নেই। তাতে শুধু এ পার্থিব জীবন-যাপনের জন্য কতগুলো আচরণবিধি লেখা আছে।
ইহুদিদের ধর্মশিক্ষার মূল কথা হল এমন কতগুলো নীতি-উপদেশ যার দ্বারা তারা তাদের জাতিগত রক্তের শুচিতা অক্ষুণ্ণ রেখে জগতের অন্যান্য জাতিদের সঙ্গে মিশতে পারে। ইহুদি অ-ইহুদিদের সঙ্গে কিভাবে মেলামেশা করবে তার কথা সব বলা আছে। কিন্তু ইহুদিদের ধর্মশিক্ষার মধ্যে কোন নীতিকথা নেই, আছে শুধু অর্থনীতির কথা। এ কারণে ইহুদিদের ধর্ম আর্যদের ধর্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। এ কারণেই খৃষ্টধর্মের প্রবর্তক ইহুদি জাতি সম্পর্কে যথাযোগ্য মূল্যায়ন করে এবং সমস্ত মানবজাতির শত্রু এ জাতিকে ঈশ্বরের স্বর্গরাজ্য হতে বিতাড়িত করে। তার কারণ ইহুদিরা সব সময় ধর্মকে ব্যবসা ও কাজকারবারের কাজে নির্লজ্জভাবে ব্যবহার করত। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ইহুদি জাতির লোকেরা খৃষ্টকে ক্রুশবিদ্ধ করে, সেই খ্রিস্টানরা পর্যন্ত ইহুদি জাতির লোকদের কাছে নির্বাচনের সময় ভোটভিক্ষা করতে যায়। এমন কি তারা নাস্তিক ইহুদি জাতির সঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক চুক্তি সম্পাদন করে সমগ্র খ্রিস্টান জাতির বিশুদ্ধিকরণ করে থাকে।
ইহুদিদের এ ধর্মগত ভণ্ডামীর ওপর আরো অনেক মিথ্যা পরবর্তীকালে জমা হতে থাকে। এসব মিথ্যা অন্যতম হল ইহুদিদের ভাষা। ইহুদিদের কাছে ভাষা মানুষের মনের গভীর ভাব ও চিন্তা-ভাবনা প্রকাশের মাধ্যমে নয়। সে ভাব ও ভাবনা ঢেকে রাখার উপায়মাত্র। ইহুদিরা যতদিন অন্য কোন জাতিকে জয় করতে পারে না ততদিন তাদের দেশে গিয়ে তাদের ভাষা রপ্ত করে।
ইহুদি জাতির সমগ্র অস্তিতুটি যে মিথ্যায় ভরা তার প্রমাণ হল ইহুদিদের ধর্মশাস্ত্র কোন্ ধ্যানতন্ময়তা থেকে এ শাস্ত্ৰবাক্যের উদ্ভব তা কেউ জানে না। তবে এর থেকে ইহুদিদের ভাবধারা ও জাতীয় চরিত্রের অনেক বৈশিষ্ট্যের কথা জানা যায়। তার সঙ্গে যে লক্ষ্যের দিকে তাদের সকল জাতীয় কর্মধারা প্রবাহিত হচ্ছে তাও জানা যায়। এমন কি তাদের সংবাদপত্রগুলোও এ শাস্ত্রের কোন মহত্ত্ব স্বীকার করতে চায় না। যে মুহূর্তে বিশ্বের মানুষ এ শাস্ত্র হাতে পাবে এবং তাতে কি আছে তা সব জানতে পারবে সেই মুহূর্তে ইহুদি জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে এ পৃথিবী থেকে।
ইহুদিজাতিকে ভাল করে জানতে হলে কয়েক শতাব্দী আগে থেকে তাদের গতিবিধির কথা জানতে হবে। তাদের এ গতিবিধির ইতিহাসটিকে কয়েকটা স্তর বা পর্যায়ে ভাগ করে দেখালে ভাল হয়।
জার্মানিয়া নামে অভিহিত প্রথম কয়েকজন ইহুদি আসে রোমান আক্রমণের সময়। তারা আসে বণিকের বেশে, আপন জাতীয়তা গোপন করে। ইহুদিরা যখন আর্যদের ঘনিষ্ট সম্পর্কে আসে একমাত্র তখনি তাদের কিছু উন্নতি দেখা যায়।
(ক) স্থায়ী বসতি স্থাপিত হওয়া মাত্র ইহুদিরা সেখানে বণিকের বেশে উপস্থিত হয়। তারা তখন সাধারণত দু’টি কারণে তাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে সমর্থ হয়। প্রথমত তারা অন্যান্য জাতির ভাষা জানত না। একমাত্র ব্যবসাগত ব্যাপার ছাড়া আর অন্য বিষয়ে কোন কথা বলত না বা মিশত না কারো সঙ্গে। দ্বিতীয়ত তাদের স্বভাবটা ছলচাতুর্যে ভরা ছিল বলে কারো সঙ্গে মিল হত না তাদের।
(খ) ধীরে ধীরে তারা স্থানীয় অর্থনৈতিক কর্মতৎপরতায় অংশগ্রহণ করে। কিন্তু অর্থনীতির ক্ষেত্রে তারা কোন উৎপাদকের ভূমিকা গ্রহণ করেনি, গ্রহণ করে দালালের ভূমিকা। হাজার হাজার বছর ধরে ব্যবসা করা সত্ত্বেও তাদের ব্যবসাগত চাতুর্য আর্যদের হার মানিয়ে দেয়। কারণ অর্থনীতির ক্ষেত্রেও আর্যরা সবসময় সততা মেনে চলত। কাজেই ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপারটা যেন ইহুদিদেরই একচেটিয়া কারবারে পরিণত হয়। তাছাড়া তারা চড়া সুদে টাকা দিতে থাকে। ধার করা ঢাকায় সুদের প্রবর্তন তাদেরই কীর্তি। এ সুদপ্রথার অন্তর্নিহিত জটিলতার কথাটা ভেবে দেখা হয়নি, সাময়িক সুবিধার জন্য এ প্রথা তখন মেনে নিয়েছিল সবাই।
(গ) এভাবে ইহুদিরা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলে নিজেদের। ছোট বড় বিভিন্ন শহরের এক একটা অংশে বসতি গড়ে তোলে তারা। এক একটা রাষ্ট্রের মধ্যে গড়ে ওঠে এক একটা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। তারা ভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপারটাতে যেন একমাত্র তাদেরই অধিকার, আর এ অধিকার বশে প্রমত্ত হয়ে তার স্বর্ণ সুযোগ নিতে থাকে।
(ঘ) ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একচেটিয়া আধিপত্য লাভ করলেও ইহুদিরা যুদ্ধের কারবারের জন্য হেয় হয়ে ওঠে জনগণের কাছে। ক্রমে ইহুদিরা ভূ-সম্পত্তি অর্থাৎ জমি জায়গা প্রভৃতি নিয়েও কেনাবেচা করা শুরু করে। তারা অনেক জমি কিনে কৃষকদের খাজনার বন্দোবস্ত করে বিলি করতে থাকে। যে কৃষক তাদের বেশি খাজনা দিত, সেই কৃষক জমি চাষ করতে পারত। ইহুদিরা কিন্তু নিজেরা জমি চাষ করত না। তারা শুধু জমি নিয়ে ব্যবসা করত। ক্রমে ইহুদিদের অত্যাচার বেড়ে উঠলে ঋণগ্রস্ত জনগণ বিদ্রোহী হয়ে ওঠে তাদের বিরুদ্ধে। তৎক্ষণাৎ স্থানীয় অধিবাসীরা ইহুদিদের স্বরূপ বুঝতে পারে। তাদের সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করে। ইহুদিদের জাতীয় চরিত্রের অশুভ বৈশিষ্ট্যগুলোকে তখন তারা খুঁটিয়ে দেখতে থাকে।
চরম দুরবস্থার মধ্যে পড়ে জনগণ প্রচণ্ডভাবে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং ইহুদিদের বিষয়সম্পত্তি জোর করে কেড়ে নেয়। তখন তারা ইহুদিদের মনেপ্রাণে ঘৃণা করতে থাকে এবং তাদের দেশে ইহুদিদের উপস্থিতি বিপজ্জনক বলে ভাবতে শুরু করে।
(ঙ) ইহুদিরা এবার খোলাখুলিভাবে আপন স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করে। তারা সরকারকে হাত করে, তোষামোদ দ্বারা প্রশাসনের লোকজনদের বশীকৃত করে টাকা উৎকোচ দ্বারা অনেক অসৎ কাজ করিয়ে নেয়। এভাবে তারা শোষণের সুবিধা করে নেয়। ক্রুদ্ধ জনগণের কোপে পড়ে তারা একসময় বিতাড়িত হতে বাধ্য হলেও আবার তারা ফিরে আসে। আবার তারা সেই ঘৃণ্য ব্যবসা শুরু করে দরিদ্র জনগণকে শোষণ করতে থাকে।
এ ব্যাপারে ইহুদিরা যাতে বেশি দূর এগোতে না পারে তার জন্য আইন প্রণয়ন করে কোন ভূ-সম্পত্তির অধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়।
(চ) রাজা মহারাজাদের শক্তি যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে ইহুদিরা তাতেই তাদের দিকে ঢলে। তাদের তোষামোদ করতে থাকে। তাদের কাছ থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ ও সুবিধে লাভের চেষ্টা করে। মোটা মোটা টাকার বিনিময়ে রাজা রাজরাও তাদের সেইসব সুযোগ দিতে থাকে। কিন্তু ধূর্ত ইহুদিরা রাজাদের যত টাকাই দিক, অল্প সময়ের মধ্যে তারা কম শোষণ করে না। রাজাদের টাকার দরকার হলেই নতুন সুবিধাভের জন্য ইহুদিরা আবার তাদের টাকা দিত। এভাবে রক্তচোষা জেঁকের মত একধার থেকে সকল শ্রেণীর লোককে শোষণ করত তারা।
এ বিষয়ে জার্মান রাজাদের ভূমিকা ইহুদিদের মতই ছিল সমান ঘৃণ্য। তাদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই এতখানি উদ্ধত হয়ে ওঠে ইহুদিরা এবং তাদের জন্য জার্মান জনগণ ইহুদিদের শোষণ থেকে মুক্ত করতে পারছিল না নিজেদের। পরে অবশ্য জার্মান রাজারা শয়তানদের কাছ থেকে নিজেদের বিক্রি করে বা চিনে নিয়ে তার প্রতিফল হাতে হাতে পায়। শয়তানদের প্রলোভনে তাদের দেশের জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে একথা বুঝতে পারে।
(ছ) এভাবে জার্মান রাজারা ইহুদিদের প্রলোভনে ধরা দিয়ে শ্রদ্ধা ও সম্মান হারিয়ে ফেলে। শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভের পরিবর্তে তাদের ঘৃণা করতে থাকে দেশের জনগণ। কারণ রাজারা তাদের প্রজাদের স্বার্থ রক্ষা করতে সমর্থ তো হয়ইনি, বরং প্রকারান্তরে দেশের জনগণকে শোষণ করতে সাহায্য করত ইহুদিদের। এদিকে চতুর ইহুদিরা বুঝতে পেরেছিল জার্মান রাজাদের পতন আসন্ন। অমিতব্যয়ী জার্মান রাজারা যে অর্থ অপব্যয় করে উড়িয়ে দিয়েছে, সেই অর্থ জোগাড়ের জন্য তাদের একজনকে ধরে নিজেদের উন্নতি ত্বরান্বিত করে তুলতো তারা। টাকা দিয়ে তারা বড় বড় সম্পদও লাভ করতে থাকে। সমগ্র জার্মান সমাজ দুষিত হয়ে পড়ে ঘরে বাইরে।
(জ) এ সময় হঠাৎ এক রূপান্তর দেখা দেয় ইহুদিদের জগতে। এতদিন তারা সবদিক দিয়ে তাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে চলেছিল। কিন্তু এবার তারা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। খ্রিস্টান চার্চের যাজকেরা এক নতুন মানবসন্তান লাভ করে। ফ্রেডারিক দ্য গ্রেট-এর আমলে কিন্তু জার্মান জনসাধারণ ইহুদিদের ইহুদি বলেই জানতো। সরকার গঠন করে খ্রিস্টান ও ইহুদিদের মধ্যে বিবাহ বন্ধ করতে না পারায় প্রতিবাদে ফেটে পড়ে গ্রেট। গ্রেটকে এককথায় কিছুতেই প্রতিক্রিয়াশীল বলা যেতে পারে না। রাজসভাতে ইহুদিরা যতই সম্মান পাক দেশের জনগণ কিন্তু তাদের বিদেশী বলেই মনে করত।
কিন্তু ইহুদি এবার জার্মান ভাষা শিক্ষা করতে শুরু করে। ব্যক্তিগত রক্তের সংমিশ্রণ না ঘটিয়েও তারা অপর জাতির ভাষা শিক্ষা করতে থাকে। কিন্তু এ ভাষা শিক্ষার ফলে তাদের অন্তরসত্তার বা স্বভাবের কোন পরিবর্তন হয় না। তারা এ নতুন ভাষার মাধ্যমে তাদের প্রাচীন ভাবধারা প্রকাশ করতে থাকে।
কিন্তু ইহুদিরা কেন জার্মান ভাষা শিক্ষা করতে গেল তার কারণটা খুঁজে বার করা এমন কিছু কঠিন নয়। ইহুদিরাই জার্মান রাজশক্তির পতন ঘটিয়েছিল। এখন শুধু তাদের ওপর নির্ভর করে থাকাটা উচিত হবে না। তখন তারা যদি সমাজের সর্বস্তরে তাদের অর্থনৈতিক আধিপত্যকে প্রসারিত করে দিতে চায় তাহলে দেশের নাগরিকত্ব অর্জন করতে হবে। সমাজের বুকে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবার জন্য এক নতুন ভিত্তিভূমি খাড়া করতে হবে আর এ জন্য চাই ভাষাশিক্ষা।
তারা একই সঙ্গে তাই আত্মসংরক্ষণ এবং আত্মপ্রসাদের নীতি অবলম্বন করতে চায়। তারা যতই ওপরে উঠতে থাকে ততই তাদের উচ্চাভিলাষের উচ্চতাটা মোহময় হয়ে ওঠে তাদের চোখের সামনে। একদিন প্রাচীনকালে বিশ্বজয়ের ও বিশ্বশাসনের যে অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি তাদের গোচর হয়েছিল, তখন সেই সুযোগের অপূর্বক্ষণ এসে গেছে বলে মনে হয় তাদের।
এভাবে রাজসভা থেকে জাতীয় জীবনের স্তরে ছাড়পত্র পায় ইহুদিরা। কিন্তু রাজসভা থেকে ইহুদিরা বিদায় নিলেও সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকদের সঙ্গে তারা যোগাযোগ রেখে যেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে তাদের মানসিক রূপান্তরের কথাটা জনসাধারণকে জানাতে চাইল যে তারা জনসাধারণের মঙ্গল এবং উন্নতি চায়। তারা তখন সারা পৃথিবী জুড়ে ঢাক পিটিয়ে প্রচার করতে লাগল তারা জনগণের দুঃখ কষ্টে গভীরভাবে দুঃখিত এবং আন্তরিকতার সঙ্গে তারা এর প্রতিকার করতে ইচ্ছুক। আরো বলতে লাগল যে তাদের ওপর সকলে অবিচার করে এসেছে। অত্যাচার করে এসেছে। অনেক নির্বোধ লোক তাদের এ কথায় বিশ্বাস করে তাদের করুণার চোখে দেখতে লাগল।
ফলে অল্পদিনের মধ্যে জগতের সবাই জানল ইহুদিরা একেবারে বদলে গেছে। রূপান্তরিত হয়ে গেছে তাদের সত্তা। এমন উৎসাহের সঙ্গে ইহুদিরা মানব জাতির উন্নতি ও অগ্রগতির কথা বলতে লাগল যে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেল জগত্বাসী। কিন্তু সেই বিশ্বাসপ্রবণ নির্বোধেরা বুঝল না তাদের এ কপট পরদুঃখকাতরতা ও পরোপকার প্রবৃত্তিগুলো ইহুদিরা দামী সারের মত জগৎ জুড়ে ছড়িয়ে রেখেছে এক বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে। এ সারের ফলস্বরূপ তারা একদিন সেই জমিতে অনেক ভাল ফসল তুলবে।
ইহুদিরা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ঢোকার পর থেকে নানারকমের সমস্যা দেখা দেয়। তারা বিভিন্ন দেশের স্টক এক্সচেঞ্জে শেয়ার কেনাবেচা শুরু করে। যৌথ কারবারের অংশীদার হয়। অতি লাভের আশায় তারা জাতীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে মালিক শ্রমিকের মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে দেয়। এ বিরোধ কালক্রমে রাজনৈতিক শ্রেণী সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করে।
সর্বশেষে ইহুদিরা স্টক এক্সচেঞ্জে তাদের প্রাধান্য থাকার জন্য অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। বিভিন্ন কাজ কারবারের মালিকানা না পেলেও বিভিন্নভাবে এবং কৌশলে শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রিত করতে লাগল।
শুধু অর্থনীতির ক্ষেত্রে নয়, রাজনীতির ক্ষেত্রেও এবার প্রভাব বিস্তার করতে থাকে ইহুদিরা এবং এ উদ্দেশ্যে তারা জাতিগত ও নাগরিক বাধাগুলো দূরীকরণের কাজে সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তার ধর্মগত সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতে থাকে। এ ব্যাপারে তাদের দ্বারা গঠিত ভ্রাতৃত্ব সংঘ তাদের সহায়তা করে। সরকারি কর্মচারী থেকে শুরু করে অনেক বুর্জোয়া শিল্পপতিও তাদের ফাঁদে ধরা দেয়।
ইহুদিদের এসব পাতা ফাঁদে এতদিন শুধু সমাজে উঁচু তলার লোকরাই ধরা দিয়ে আসছিল। যে সাধারণ জনগণ নিজেদের বুঝতে চেষ্টা করেছিল, নিজেদের স্বাধীনতা ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রামশালী হয়ে উঠছিল, সদাজাগ্রত এ জনগণ এতদিন দূরে ছিল তাদের পাতা ফাঁদ থেকে। কিন্তু ইহুদিরা জানত সমাজের গভীরতর স্তরে অনুপ্রবিষ্ট হতে হলে এ বৃহত্তর জনসাধারণের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে হবে।
এ উদ্দেশ্যে তারা ভ্রাতৃত্ব সংঘের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রগুলোও করায়ত্ত করতে চায়। জনমত প্রচারের যন্ত্রকে হাত করে কৌশলে লেখকের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে তারা। তারা কোন খ্রিস্টান মেয়েকে কিছুতেই বিয়ে করত না, অথচ খ্রিস্টানরা ইহুদি মেয়ে বিয়ে করত এবং সেক্ষেত্রে সেই বিয়ের ফলে জাত সন্তানদের ইহুদি বলে চালানো যেত। এভাবে তারা সব জাতের গর্ব খর্ব করতে চাইছিল। নিজেরা অন্য কোন জাতির মেয়ে ঘরে না এনে নিজেদের জাতিগত রক্তের শুচিতা রক্ষা করে যাচ্ছিল।
ইহুদিদের চাতুরী ও ধুর্তামি সত্ত্বেও সংবাদপত্রগুলো প্রচার করে বেড়াচ্ছিল যে ইহুদিরা মূলগতভাবে সৎ লোক, জনগণের ওপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য তারা গণতন্ত্রের প্রসারের জন্য জোর প্রচার চালাতে লাগল। কারণ তারা জানত একমাত্র সংসদীয় গণতন্ত্রই তাদের উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে সহায়ক হয়ে উঠবে। একমাত্র এ শাসনযন্ত্রেই ব্যক্তিগত গুণাবলীর কোন দাম দেওয়া হয় না। এবং অপদার্থ ও অযোগ্য লোকদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।
এর ফলে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটে।
এক অভাবনীয় অর্থনৈতিক পরিবর্তন সমাজের কাঠামোটাকেই পাল্টে দেয়। আগে যেসব কর্মী কুটিরশিল্পে কাজ করত তারা কারখানা শ্রমিকের কাজ করতে এসে নিজেদের স্বাধীনতা হারিয়ে সর্বহারায় পরিণত হয়। কারখানা শ্রমিকের জীবনের সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হল এ যে ভবিষ্যত বার্ধক্য জীবনের জন্য কোন ব্যবস্থা করতে পারে তারা।
শিল্প বিপ্লবের ফলে যেসব কলকারখানা গড়ে উঠতে লাগল তাতে গ্রাম থেকে দলে দলে লোক এসে যোগদান করতে থাকে শ্রমিক হিসেবে। এরা আগে গ্রামে কুটিরশিল্পের কাজ করত। শহরের শ্রমিক জীবনের সঙ্গে অভ্যস্ত ছিল না তারা। তার ওপর কারখানার মালিকদের কাছ থেকে কোন সহানুভূতি পেত না। গ্রামের জমিতে যে সকল কৃষক মজুর কাজ করে তাদের সঙ্গে জমির মালিকদের সম্পর্ক ভালো; যেখানে মালিকরাও শ্রমিকদের সঙ্গে একসঙ্গে চাষের কাজ করে। মালিক শ্রমিকের কোন ভেদাভেদ নেই। কিন্তু শহরে কায়িক শ্রমকে ঘৃণার চোখে দেখা হয় বলে সেখানে কলকারখানার মালিকেরা শ্রমিকদের ঘৃণার চোখে দেখে, তাদের মানুষ বলে মনেই করে না।
কিন্তু কায়িকশ্রমের এ ঘৃণা আর শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের মধ্যে ভেদজ্ঞানের প্রবর্তন একান্তভাবেই ইহুদিদের অবদান। এ ধরনের ভেদনীতি জার্মানজাতির মধ্যে কোনদিন ছিল না।
এর ফলে যে শোষিত ও অবহেলিত শ্রমিকশ্রেণীর উদ্ভব হল সমাজে, তারা কিন্তু মানুষ হিসেবে নিকৃষ্ট নয় মোটেই। তারাও যে বৃহত্তর সমাজের এক বিশেষ অপরিহার্য অঙ্গ একথা আমাদের অবশ্যই অচিরে একদিন বুঝতে হবে। তাদের কাছে টেনে নেব আপন করে, অথবা দূরে ঠেলে দেব, সরিয়ে রাখব অন্ত্যজশ্রেণী হিসেবে সে প্রশ্নের মীমাংসা করতে হবে।
এ শ্রমিকশ্রেণীর ওপর আধুনিক সভ্যতার ঘৃণ্য কুফল এ যুগে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। কায়িক শ্রমের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল এসব লোক এ যুগের শান্তিবাদীদের অপ্রকৃতিস্থ দুর্বলতার শিকার হয়ে পড়েনি। তাদের মধ্যে যথেষ্ট সংগ্রামশীল প্রবৃত্তি আছে।
আমাদের সমাজের বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এ নতুন অবস্থা সম্পর্কে উদাসীন থাকার জন্য ইহুদিরা এর পূর্ণ সুযোগ নিতে ছাড়ে না। তারা পুঁজিবাদী শোষণের এমন যন্ত্র গড়ে তোলে যার ফলে শ্রমিক মালিকের সম্পর্কে আরো অবনতি ঘটে। তখন মিথ্যাবাদী ইহুদিরা নির্দোষিতার নামাবলী গায়ে দিয়ে বেড়াতে থাকে।
একদিন এ ইহুদিরাই সামন্তশ্রেণীর বিরুদ্ধে পুঁজিবাদীদের সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিল; সেই ইহুদিরাই আজ শ্রমিক মালিকের মধ্যে ভেদনীতি জাগিয়ে বুর্জোয়া মালিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ক্ষেপিয়ে তোলে। ভাবে এর দ্বারা শ্রমিক সমাজের সমর্থন ও শ্রদ্ধা লাভ করে তাদের ওপর সর্বদা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে।
অথচ শ্রমিকেরা বুঝতে পারে না এক্ষেত্রেও তারা ধূর্ত ইহুদিদের উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হয়ে কাজ করেছে। স্টক এক্সচেঞ্জের ওপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে যে আন্তর্জাতিক পুঁজিকে হাত করেছে ইহুদিরা; বিভিন্ন দেশের শ্রমিকশ্রেণী স্বদেশের জাতীয় পুঁজির গায়ে আঘাত হেনে প্রকারান্তরে আন্তর্জাতিক পুঁজির পুষ্টি ও সহায়তা সাধন করে চলেছে।
প্রথম প্রথম ইহুদিরা এক বিরাট ভণ্ডামীর সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর দুঃখে মায়াকান্না কেঁদে তাদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর ভাণ করে। যে পরদুঃখকাতরতা ও সামাজিক মঙ্গলের জন্য ব্যাকুলতা আর্যদের জাতীয় চরিত্রের একটি মহৎ গুণ, সেইগুণের প্রমাণ দেবার চেষ্টা করে তারা। তারপর তাদের তথাকথিত সামাজিক অন্যায় অপসারণের জন্য সংগ্রামকে এক দার্শনীক রূপ দান করার মতলব নেয়। আর তার জন্যই মার্কসবাদের উদ্ভাবন।
ইহুদিরা এ তত্ত্ব সমস্বরে বিশ্বে প্রচার করে বেড়ালেও অনেক বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত ব্যক্তি এ তত্ত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করে। কারণ তারা বলে এ দার্শনিক তত্ত্বকথার অন্তরালে এক শয়তানসূলভ প্রবৃত্তি লুকিয়ে আছে। এ তত্ত্বের মধ্যে মানবিক যুক্তি, মানবিক অবাস্তবতা ও অযৌক্তিকতা এমনভাবে মিশে আছে যাতে অবাস্তব অযৌক্তিক দিকটির প্রকাশ দেখা যায় সর্বত্র। যে ব্যক্তিগত ও জাতিগত যোগ্যতা মানবসভ্যতার মূল ভিত্তি, সে যোগ্যতার সকল গুরুত্বকে অস্বীকার করে এ তত্ত্ব সভ্যতার ভিত্তিমূলেই আঘাত হানে। এভাবে ব্যক্তিগত ও জাতিগত ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্যের ধারণাকে নস্যাৎ করে দেওয়ায় ইহুদিদের সামাজিক আধিপত্যলাভের সঙ্গে বাধাগুলোও অপসারিত হয়।
মার্কসবাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিকগুলো অবাস্তব। এর মধ্যে যে যুক্তি আছে তা আপাত দৃষ্টিতে জোরালো মনে হলেও আসলে তার কোন ভিত্তি নেই, যাদের বুদ্ধিবৃত্তি কম, অর্থনীতি সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই, তারাই এ মতবাদের সমর্থক।
এ মতবাদকে অবলম্বন করে ইহুদিদের নেতৃত্বে এক শ্রেণীর শ্রমিক এক ধরনের আন্দোলন শুরু করে। ওপর ওপর এ আন্দোলন শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে চাইলেও আসলে অ-ইহুদি জাতিদের ধ্বংস করাই ছিল সেই আন্দোলনের উদ্দেশ্য।
একদিন ভ্রাতৃত্ব সংঘের লোকেরা বিশ্বপ্রেম প্রচারের মাধ্যমে জাতীয় আত্মরক্ষার নীতিকে বিকল করে দেয়। আজ ইহুদিদের পরিচালিত সংবাদ পত্রগুলি সেই প্রচারের ভার নিয়েছে। এবং শ্রমিক ও বুর্জোয়া শ্রেণীর সম্পর্ককে দূষিত করার চেষ্টা করছে। তার ওপর মার্কসবাদী উগ্রপন্থীরা তাদের বিরোধী পক্ষের ওপর নির্মমভাবে আঘাত চালিয়ে আসুরিক শক্তির পরিচয় দিচ্ছে। মার্কসবাদী শক্তিলাভের সম্মিলিত আক্রমণের ফলে অনেক রাস্ত্রীয় শক্তির ভিত্তি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীর ওপরে ইহুদিরা কৌশলে প্রভাব বিস্তার করে। এসব অত্যুৎসাহী উগ্রপন্থী মার্কসবাদী সমাজের ছোট বড় কাউকেই মানতে চায় না; কাউকেই মানুষ বলে জ্ঞান করে না।
ইহুদিদের দ্বারা পরিচালিত শ্রেণী-সগ্রামের রূপটি প্রকাশ করতে গেলে এ দাঁড়াবে; সারা বিশ্বে অর্থনৈতিক আধিপত্য লাভ করে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হতে পারেনি ইহুদিরা। তারা রাজনৈতিক আধিপত্য লাভের জন্য সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এ উদ্দেশ্যে তারা মার্কসীয় তত্ত্বটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করে দেখে। সেই দুটো ভাগ হল রাজনৈতিক আন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এ দুটি আন্দোলন আলাদা হলেও আসলে কিন্তু তারা একই উদ্দেশ্যসঞ্জাত।
স্বার্থপর, অর্থলোভী, সংকীর্ণমনা পুঁজিপতি বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে পরিচালিত শ্রমিকশ্রেণীর সগ্রামে ট্রেড ইউনিয়নগুলো শ্রমিকদের রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে চলে। শ্রমিকেরা যতদিন না মানুষের মত বাঁচার জন্য যা দরকার তা না পায় ততদিন তারা সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। শুধু তাই নয় শ্রমিকদের কাজের সময় কম করে দেওয়া, শিশু শ্রমিক নেওয়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া প্রভৃতি ব্যাপারে আইন প্রণয়নে বাধা দেয় তারা। বুর্জোয়ারা যখন এভাবে শ্রমিকদের সংগ্রামে বাধা দিতে থাকে তখন কঠিন প্রকৃতির ইহুদিরা নিপীড়িত শ্রমিক-শ্রেণীর পক্ষ অবলম্বন করে সমগ্র ব্যাপারটা নিজেদের হাতে তুলে নেওয়ায় রাতারাতি ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার নেতা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ তারা জানত এভাবে তারা বিরাট শ্রমিকশ্রেণীকে তাদের সমর্থক হিসেবে কাজে লাগাতে পারবে। কিন্তু তাদের আসল উদ্দেশ্য কিন্তু শ্রমিকদের উন্নতির বা অগ্রগতি ছিল না; তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকদের অর্থনৈতিক যুদ্ধে এক সশস্ত্র হাতিয়াররূপে ব্যবহার করে জাতীয় অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র ও উন্নতিকে ধ্বংস করে দেওয়া। তাদের এ উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায়ে তারা শ্রমিকদের কাছে এমন সব শর্ত উত্থাপন করত যে সেসব শর্ত মেনে নেওয়া কখনই কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তারা জানত এসব শর্ত কেউ পূরণ করতে পারবে না। তা করা সম্ভবও নয়। তবু শ্রমিকদের সংগ্রামকে ধ্বংস করার জন্যই তারা এমন সব অসঙ্গত দাবি তোলে। এভাবে আসলে তারা জাতীয় পর্যায়ে এক বিরাট অশান্তি জাগিয়ে রাখতে চায়।
ইহুদিরা তাই ট্রেড ইউনিয়নের অবিসম্বাদিত নেতা হয়ে যায়। যতদিন পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে জোর প্রচারকার্য চালানো না হয়, ততদিন তারা এভাবেই নেতা হয়ে যাবে। যতদিন না জনগণ ঠিক মত বুঝতে পারে এবং ইহুদিদের ছল চাতুরীর কথা জানতে না পারে ততদিন ইহুদিদের বড় বড় প্রতিশ্রুতির কথায় বিশ্বাস করে যাবেই।
সহজে এবং স্বাভাবিকভাবেই ইহুদিরা তাদের প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বীদের সরিয়ে দেয় এ ক্ষেত্র থেকে। ক্রমে তারা তাদের স্বাভাবিক নিষ্ঠুরতার বশে ট্রেড-ইউনিয়ন সংস্থাগুলোকে বলপ্রয়োগের মাধ্যম হিসেবে পরিণত করে। ইহুদিদের একনায়কতন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ না করে যারা তাদের বাধা দেয়, এক ব্যাপক সন্ত্রাস সৃষ্টি করে তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয় ইহুদিরা।
ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন মূলত অর্থনৈতিক আন্দোলন হলেও এ আন্দোলনকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে থাকে ইহুদিরা। ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থার সদস্যরা রাজনৈতিক মিছিল বার করে এবং রাজনৈতিক কার্যাবলীতে তৎপর হয়ে ওঠে। অবশেষে শ্রমিকরা ধর্মঘট ঘোষণা করে তাদের অর্থনৈতিক আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দালনে পরিণত করে।
এ কাজে তাদের ইহুদিদের দ্বারা প্রভাবিত সংবাদপত্রগুলি সাহায্য করে। সংবাদপত্রগুলি জনসাধারণের মঙ্গল সাধনের কোন চেষ্টা না করে তাদের মধ্যে কু-প্রবৃত্তি সঞ্চারিত করার চেষ্টা করে। এ সংবাদপত্রগুলোই নানারকম মিথ্যা প্রচারের দ্বারা জাতীয় অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার ভিত্তিটিকে বিপর্যস্ত করে দেয়।
সুচতুর ইহুদিদের কেউ আক্রমণ করার আগেই তারা ওদের আক্রমণ করে। যারা ওদের আক্রমণ করতে আসে ওরা শুধু ওদের আক্রমণ করে না, যারা ওদের আক্রমণে বাধা দেয় আত্মরক্ষার খাতিরে ওরা তাদেরও শক্ত বলে মনে করে। ইহুদিদের আসল মনোভাব ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সাধারণ জনগণের কোন জ্ঞান না থাকার ফলে তারা সহজেই ইহুদিদের কু-প্রকৃতি ও কু-অভিসন্ধির শিকার হয়ে ওঠে। সরলতা ও অজ্ঞতাবশত সাধারণ মানুষ বিশ্বাসপ্রবণ হয়ে থাকে এবং তারা সহজে যে কোন প্রচারে কান দেয় ও তা বিশ্বাস করে। তারা বুঝতে পারে না ইহুদিরা মার্কসবাদকে তাদের এক অশুভ উদ্দেশ্য পূরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে চায়।
তখন ইহুদিরা প্যালেস্টাইনে এক সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করে এমনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে নিজেদের যে তারা তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ ও তথ্য ধারাগুলো স্বাচ্ছন্দে মুক্তকণ্ঠে প্রচার করে চলে। আসলে তারা নিজেদের ফরাসী জার্মান প্রভৃতি ভিন্ন জাতির লোক বলে সরলমনা সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করতে চাইছে। কিন্তু রাষ্ট্রের খাতিরে তারা রাষ্ট্র গঠন করতে চায় না। বস্তুত তারা রাষ্ট্রের নামের একটি বৈধ ও সার্বভৌম সংগঠনের মাধ্যমে সারা বিশ্বব্যাপী প্রতারণা ও জুয়াচুরির জাল বিস্তার করতে চায়। জুয়াচুরি ও প্রতারণার এক বিরাট শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করতে আগ্রহী।
তার ওপর কৃষ্ণকেশ ব্যভিচারী ইহুদী যুবকেরা পথের ধারে ঘন্টার পর ঘণ্টা ধরে বসে থেকে বিজাতীয় মেয়েদের শালীনতা নষ্ট করতে চায়। তাদের জারজ নানা সংমিশ্রিত গরল ঢেলে সেইসব নিরীহ মেয়েদের রক্তকে কলুষিত করার চেষ্টা করে। কারণ তারা জানে যে জাতি তাদের জাতিগত রক্তের শুচিতা সম্পর্কে সচেতন তারা কখনই ইহুদীদের আদিপত্য মেনে নেবে না। অবৈধ জারজ সন্তানে পরিপূর্ণ কোন জাতি ছাড়া অন্য কোন জাতির ওপর ইহুদীরা কখনই প্রভূত্ব করতে পারবে না।
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহুদীরা গণতন্ত্রের জায়গায় সর্বহারার একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। কারণ তারা জানে মার্কসবাদের পতাকাতলে সাধারণ জনগণকে সংঘবদ্ধ করে একনায়কতন্ত্রের ধাঁচে তাদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে আসুরিক শক্তির দ্বারা দেশ শাসন করা সহজ হবে তাদের পক্ষে। যেসব শক্তিশালী জাতি ইহুদীদের প্রভাব মানতে চায় না, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে সেইসব জাতির চারদিকে শত্রু খাড়া করে তুলেছে।
অর্থনীতি ও রাজনীতি দুদিক থেকেই বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতিগুলির বনিয়াদ ধ্বংস করতে চায় ইহুদী। রাষ্ট্রায়ত্ত শরিকানা শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষতিসাধন করে তারা যেমন জাতীয় অর্থনীতির ধ্বংস করতে চায়, তেমনি সরকার ও জনগণের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে জাতির প্রতিরক্ষাগত শক্তির ভিত্তিকে নষ্ট করে ফেলতেও সচেষ্ট থাকে।
জাতীয় সংস্কৃতির মূলেও আঘাত হানতে চায় তারা। শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুন্দর ও মহত্বের ধারণাটিকে জাতিপ্ৰীতির নাম করে নষ্ট করে ফেলে সাধারণ মানুষের মনকে তাদের মত নিচ ও সংকীর্ণ করে তোলে।
ধর্মের ক্ষেত্রটিও তারা প্রহসনের এক রঙ্গভূমিতে পরিণত করে। নীতিবোধ ও শালীনতাবোধ প্রভৃতিকে প্রাচীন কুসংস্কার বলে অভিহিত করে জাতির নৈতিক ধারণাকে নামিয়ে আনতে চায় তারা।
যখনি ইহুদীরা রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করে, তখনই তারা সব অবগুণ্ঠন ঝেড়ে ফেলে স্বমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। তখন তারা জনগণের হর্তাকর্তা সেজে জনগণের ওপর অত্যাচার করতে শুরু করে। সমগ্র জাতির বুদ্ধিমান ও প্রতিভাবান ব্যক্তিদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে।
রাশিয়া হল এ অত্যাচারের ভয়ঙ্কর লীলাভূমি। এ দেশে ইহুদীরা তিন কোটি লোককে হত্যা করে অথবা না খেতে দিয়ে শুকিয়ে মারে। এদের মধ্যে কিছু লোককে পীড়নমূলক কাজ করিয়ে মারা হয়। ওইসব কিছুর মূলে ছিল কিছু সংখ্যক ইহুদী যারা দেশের ওপর প্রভূত্ব করবে।
কিন্তু এর শেষ পরিণাম বড় ভয়াবহ হয়ে ওঠে। এর ফলে জনগণ অবশ্য ইহুদীদের ক্ষমতাধীনে আসে; কিন্তু পরে সেইসব অত্যাচারী ইহুদীদেরও বিদায় দেয়। শিকারের মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে নেমে আসে শিকারীর মৃত্যু।
আমরা যদি আমাদের জার্মান জাতির অধঃপতনের কারণ অনুসন্ধান করি তাহলে দেখব সেই কারণটা হল জার্মানরা ইহুদি সমস্যাটাকে তত গুরুত্ব দেয়নি। ইহুদী সমস্যা সঞ্জাত যে বিপদ সমগ্র জাতির পক্ষে এত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে সে বিপদের কথা তারা মোটেই ভাবেনি। তা যদি আগে থেকে ভাবত তাহলে ১৯১৮ সালের আগস্ট মাসের প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করাটা খুব একটা কষ্টকর হত না। আমাদের পরাজয়ের কারণ শুধু যুদ্ধক্ষেত্রের হার নয়, যে রাজনৈতিক প্রেরণা ও প্রবৃত্তি এবং নৈতিক শক্তি জাতির জীবন সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে, জাতির অস্তিত্বকে সমৃদ্ধ করে তোলে সর্বতভাবে, কয়েক দশক ধরে সুপরিকল্পিতভাবে সেই জাতীয় রাজনৈতিক প্রবৃত্তি ও নৈতিক শক্তির মূলে কুঠারাঘাত হানা হচ্ছিল।
যে শক্তি ও গুণাবলী জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি সে শক্তি ও গুণাবলীকে অবহেলা করে তাদের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণের কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা না করে জার্মানরা ভুল করেছিল। অথচ এ শক্তি ও গুণাবলী তাদের সহজাত, প্রকৃতিদত্ত।
কিন্তু যে কোন পরাজয়ই অপূরণীয় ক্ষতির বাহক নয়। যে কোন খারাপ থেকে অনেক কিছু ভাল করা যায়। যে কোন পরাজয়কে ভিত্তি করে ভবিষ্যতে জয়ের সৌধ গড়ে তোলা যায়। যুদ্ধে পরাজয় স্বীকার করে অনেক জাতি পরবর্তী যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। অনেক দুঃসহ অত্যাচারের ভেতর থেকে এমন এক অদম্য শক্তি জন্মলাভ করে যা একদিন সমস্ত অধঃপতিত জাতিকে মুক্তি এনে দেয়।
কিন্তু যে জাতি তাদের জাতিগত রক্তের শুচিতা হারিয়ে ফেলে, সেই জাতি একবার অধঃপতিত হলে আর কোনদিন উঠে দাঁড়াতে পারে না। এ রক্তের শুচিতা হানি থেকে যে ক্ষতি হয়, সে ক্ষতি আর পূরণ হয় না কোনদিন। যে কোন জাতি বা সভ্যতার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বা সাংস্কৃতিক অবক্ষয় বা অবনতির মূলে আছে এ একই কারণ। জাতিদের অন্তনিহিত শক্তি একেবারে ক্ষয় হয়ে গেলে সে জাতিকে তখন আর বাঁচানো যায় না।
এ কারণেই কোন রাজনৈতিক তৎপরতা, অর্থনৈতিক উন্নতি, সংস্কৃতির সংস্কার বা জ্ঞানের সঞ্চয়-কোন কিছুই বাঁচাতে পারেনি জার্মান জাতিকে। কোন সুফলই দান করতে পারেনি এসব কিছু। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের কপট উজ্জ্বলতা, তার কপট দৈন্য বা দূর্বলতাকে সমস্যার মূলে সে যেতে পারেনি বা তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেনি।
জার্মানির যে সব রাজনৈতিক দল দেশের জাতীয় দুরবস্থার উন্নতি ঘটাবার চেষ্টা করেছিল, তারা রোগের মূল ধারাটিকে ধরতে না পেরে শুধু তার উপসর্গগুলি সারাবার চেষ্টা করেছিল। নির্বাচনে বুর্জোয়া দলগুলি জয়লাভ করলেও মার্কসবাদী ভোটের সংখ্যা ক্রমশই বাড়তে থাকে। মার্কসবাদের বিষ সারা দেশে সব দলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।
১৯১৪ সালে যে জার্মান জাতি মহাযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সে জাতি এক সুদৃঢ় জাতীয় প্রেরণার বশবর্তী হয়ে ছুটে যায়নি। এক নির্বাপিত-প্রায় আত্মরক্ষা প্রবৃত্তির শেষ উজ্জ্বলতা ও অগ্নি-প্রেরণার বশেই সে জাতি যুদ্ধে যোগদান করে। শান্তিবাদী ও মার্কসবাদী নীতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জাতির গভীরে যে অবক্ষয় ও পক্ষাঘাত ঘিরে ধরেছিল তার বিরুদ্ধে জার্মান জাতি বাইরে জেহাদ ঘোষণা করলেও ভেতরে ভেতরে তারা ক্রমশ ক্ষয় হয়ে আসছিল।
অবশ্যই এ যুদ্ধের বিজেতাদের ঈশ্বর বিশেষ কোন পুরস্কারে ভূষিত করেনি। বরং অনুশোচনার যন্ত্রণায় ভরে ওঠে তাদের মন। আর তখনই আমরা সেই আসল সত্যটি বুঝতে পেরে তাকে স্বীকার করে নেই। এবং নতুন উদ্যমে এক প্রস্তর কঠিন ভিত্তির ওপর জাতীয় উন্নতির নতুন সৌধটির প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করি।
১১. ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট লেবার পার্টির অগ্রগতির প্রথম স্তর
এ খণ্ডের শেষের দিকে আমি আমাদের আন্দোলনের প্রথম স্তরটির কথা বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করব। কিন্তু যে আদর্শকে আমরা লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করি সে আদর্শের নিখুঁত বিশ্লেষণ এ খণ্ডে সম্ভব নয় বলে তা আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে করব; যেখানে আমাদের নীতি বা কার্যপদ্ধতির বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র শব্দটির প্রকৃত চিত্রটিও আমরা তুলে ধরব। এখানে ‘আমরা’ বলতে সেইসব লোককে বুঝি যারা একই কামনা বাসনার দ্বারা উদ্দীপিত হয় কিন্তু সকলে সেই কামনা প্রকাশ করার উপযুক্ত ভাষা খুঁজে পায় না। সমস্ত সংস্কারের মূলে আছে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমবেত একটি বাসনা, যদিও সেইসব অসংখ্য মানুষের মধ্যে থেকে প্রথমে প্রবক্তারূপে একজন এগিয়ে এসে সেই সংস্কারের কাজটি শুরু করে। সমস্ত বড় বড় সংস্কারের লক্ষ্যই হল তাই। লক্ষ লক্ষ মানুষের যেসব কামনা বাসনা যুগ যুগ ধরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গুমরে মরে, একজন প্রতিভাধর ব্যক্তি তাদের জন্য এগিয়ে এসে এক একটি সংস্কারের মধ্যে সেই কামনা বাসনাকে সার্থকভাবে রূপায়িত করে তোলে।
আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ যে এক মৌন পরিবর্তনের আশায় দিন গুনছে ব্যাকুলভাবে তা তাদের গভীর অসন্তোষ বা বিক্ষোভ থেকেই বোঝা যায়। এ অসন্তোষ বা বিক্ষোভ বিভিন্নভাবে প্রকাশিত বা পরিত্যক্ত হচ্ছে। অনেকের ক্ষোভ প্রকাশিত হয় নিবিড় হতাশা ও নিরুত্সাহের মধ্যে দিয়ে, অনেকের প্রকাশিত হয় রাগে। অনেকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে তাদের ক্ষোভের পরিচয় দেয়। আবার অনেকে কমঘেঁষা উগ্রপন্থীদের দলে যোগ দিয়ে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করে।
শেষোক্ত ব্যক্তিদের কাছেই আমাদের নবগঠিত আন্দোলনের আবেদন ছিল সবচেয়ে বেশি। যারা বর্তমান সমাজব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না হয়ে গভীর উদ্বেগ ও হতাশায় ভূগছে অথবা কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না, আমাদের আন্দোলন তাদের সকলকে এক সাংগঠনিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে চেয়েছিল।
দেশ বা জাতির উপরি পৃষ্ঠে শুধু আঁচড় না কেটে যে আন্দোলন জনগণের মনের গভীরে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল।
রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে ১৯১৮ সালে আমাদের জার্মান জাতি দুটি প্রধান অংশে বিভক্ত ছিল। তাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতর অংশটি ছিল বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা গঠিত। এ অংশের মধ্যে শ্রমজীবীদের কোন স্থান ছিল না। বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা গঠিত অংশটির একমাত্র কাজ ছিল রাষ্ট্রের স্বার্থরক্ষা করে চলা। জাতীয় স্বার্থ আর তাদের আদর্শগত ভাবধারা রক্ষা করার জন্য বুদ্ধিজীবীরা প্রতিঘাতের বিরুদ্ধে কেবল বুদ্ধিগত হাতিয়ার প্রয়োগ করে যেত। কিন্তু প্রতিঘাতের প্রধান আঘাতের সামনে এ হাতিয়ার মোটেই ফলপ্রসূ হত না।
এ মুষ্টিমেয় বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বিরুদ্ধে এক সতত সজাগ প্রতিকুলতা কাজ করে যাচ্ছিল; মার্কসবাদে দীক্ষিত শ্রমিকশ্রেণীর দ্বারা সমাজের এক বৃহত্তর অংশ এ শ্রমিকশ্রেণী তাদের প্রচণ্ড দৈহিক শক্তির দ্বারা বুদ্ধিজীবীদের সকল বাধাকে খড়কুটোর মত উড়িয়ে দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়ে উঠেছিল। তারা কোনক্রমেই জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিল না। সংখ্যাগরিষ্ঠ এ বিরাট শ্রমিকশ্রেণী দেশের স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে বিদেশী অত্যাচারী একনায়কদের স্বার্থরক্ষা করে যেত আবার এ শ্রমিক শ্রেণীর সাহায্য ছাড়া জাতীয় অভ্যুত্থানও সম্ভব ছিল না।
১৯১৮ সালে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে ছিন্নভিন্ন জাতীয় শক্তি সুসংগঠিত না হওয়া পর্যন্ত জার্মান জাতির পুনরুত্থান মোটেই সম্ভব ছিল না। আবার জাতীয় পুনরুত্থান ছাড়া বহিঃশত্রুর আক্রমণকে প্রতিহত করাও সম্ভব হয় না তাদের পক্ষে বস্তৃত জার্মানির তখন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বলতে কিছুই ছিল না। তার মানে এ নয় যে জার্মানির কোন অস্ত্রশস্ত্র ছিল না; জাতীয় আত্মসংরক্ষণের জন্য যে লৌহকঠিন সংকল্পের দরকার, যা অস্ত্রের থেকে অনেক বেশি, সেই সংকল্পের একান্ত অভাব ছিল তখন সারা দেশে।
অথচ আমাদের দেশের বামপন্থীরা বলে দেশে অন্ত্র না থাকার জন্যই তারা এ বৈদেশিক নীতি অবলম্বন করেছে। কিন্তু আসলে এ নীতি বিশ্বাসঘাতকতার নীতি। একথা সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়। মিথ্যা স্তোকবাক্য দিয়ে সাধারণ মানুষকে ভুলিয়ে রাখার ছলনামাত্র।
আমাদের দেশের দক্ষিণপন্থী রাজনীতিবিদরাও কম দায়ী নয়। তারাও একই ভৎসনার যোগ্য। তাদের শোচনীয় কাপুরুষতার জন্য ১৯১৮ সালে ইহুদীরা রাষ্ট্রক্ষমতায় আসে। এবং ক্ষমতায় আসার পর তারা জাতিকে নিরস্ত্র করে তোলে। তাদের দোষের জন্যই জার্মানি অস্ত্রহীন হয়।
সুতরাং জার্মানির জাতীয় শক্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে শুধু কারখানায় অস্ত্র নির্মাণ করলেই হবে না, জাতীয় আত্ম-সংরক্ষণ প্রবৃত্তিকে নতুন করে সঞ্জীবিত করে তুলতে হবে। কারণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্রের কৃতিত্ব বা যোগ্যতা শুধু অস্ত্রের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে জাতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ বাসনায় আর বীরত্বপূর্ণ সাহসের ওপর।
এদিক দিয়ে বৃটিশ জাতির ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বৃটিশ জাতির মধ্যে একই সঙ্গে সরকারের নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা আর জনগণের শক্তি ও সাহস লক্ষ্য করার মত। সরকারের দৃঢ়তা জনগণের শক্তি ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ বাসনা অন্যান্য জাতির তুলনায় অন্ত্রের স্বল্পতা সত্ত্বেও তাদের জাতীয় সংগ্রামকে সাফল্যের স্বর্ণচূড়ায় নিয়ে যেতে পারে।
সুতরাং দেখা যাচ্ছে জার্মানির পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জাতির মধ্যে রাজনৈতিক আত্মসংরক্ষণবোধকে নতুন করে জাগিয়ে তুলতে হবে এবং জাতীয় বিরোধী শক্তিগুলিকে জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হবে।
জার্মানিকে সার্বভৌম ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলনটিকে যদি সফল করে তুলতে হয় তাহলে দেশের সাধারণ মানুষের দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত করে তুলতে হবে। আমাদের দেশের জাতীয় বুর্জোয়ারা এমনই অপদার্থ যে তারা কোন বলিষ্ঠ অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক নীতি খাড়া করতে পারেনি। আমাদের দেশের জনগণের মতকে যুদ্ধমুখী করে তোলা যায় জোর প্রচারের মাধ্যমে, কিন্তু ইহুদী ভাইয়েরা জার্মানির পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টাকে নির্মমভাবে গুঁড়িয়ে দেবে, যেমন তারা একদিন জার্মানির সামরিক শক্তিকে গুঁড়িয়ে দেয়। দেশে মার্কসবাদীরা সুসংগঠিত এবং তাদের সংখ্যা দেড়কোটি। এ মার্কসবাদীরা শুধু যে জাতীয় কোন বৈদেশিক নীতি খাড়া করতে দিচ্ছে না তা নয়, এরা কোনক্রমেই জার্মানিকে তার রাজনৈতিক শক্তি পুনরুদ্ধার করতে দিচ্ছে না। শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই মার্কসবাদীরা এভাবে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মোটকথা যে সব রাজনৈতিক দলের নেতা দেশ ও জাতির সঙ্গে একইভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করছে তারা কোনক্রমেই জাতীয় পুনরুজ্জীবনের কোন প্রচেষ্টাকে সহ্য করতে পারছে না। তারা জাতির ইতিহাসে এ শিক্ষা দেয়, যারা জার্মানির এ অবস্থার জন্য দায়ী তাদের ওপর চরম প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত জার্মানি তার হারানো গৌরব পুনরায় উদ্ধার করতে পারবে না।
তাই জার্মানির সাবভৌমত্ব ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে শান্তিপূর্ণ ভাবে জনগণের মনের পরিবর্তন সাধন করে তাদের নিয়ে এক সংযুক্ত সংগ্রামী সংস্থা গড়ে তুলতে হবে।
বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে জনগণ স্বাধীনতার আদর্শে বিশ্বাসী হলে জার্মানিকে কিছুতেই বৈদেশিক বন্ধন থেকে মুক্ত করা যাবে না। অপর দিকে সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বোঝা যাবে শুধু ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের ওপর নির্ভর করে বিদেশী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা যায় না।
যেসব তরুণ জার্মান বুদ্ধিজীবী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদান করে ১৯১৪ সালের ক্লাইভাসের যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দেয় তাদের অভাব পরে বিশেষভাবে অনুভূত হয়। অবশ্য দেশের বিরাট সংখ্যক শ্রমিকশ্রেণী যোগদান না করলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরালো হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তার জন্য অনভিজ্ঞ অশিক্ষিত শ্রমিকশ্রেণীকে উপযুক্ত সামরিক শিক্ষাদান করা উচিত। আবার ভার্সাই শান্তিচুক্তির শর্ত অনুসারে আমাদের সমগ্র জাতিকে নিরস্ত্র অবস্থায় থাকতে হয় বলে জনগণকে সামরিক প্রশিক্ষণ দান সম্ভব নয়। দেশের স্বাধীনতার পুনরুদ্ধারের জন্য ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতিও সম্ভব নয়। দেশের মধ্যে তার জন্য প্রচুর গুপ্তচর কাজ করে যাচ্ছিল। তারা আন্তর্জাতিক মার্কসবাদের দোহাই দিয়ে জাতীয় পুনরভ্যুত্থানের পথে বাধা সৃষ্টি করছিল।
এ বাধা অপসারিত করতে হলে দেশের বৃহত্তর জনসাধারণকে অবশ্যই জাতীয় স্বাধীনতার নীতিগুলোকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে। তারা যাতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে একাজে এগিয়ে আসে তার জন্য সর্বাগ্রে চেষ্টা করতে হবে।
জাতীয় রাজনৈতিক স্বাধীনতা আগে অর্জন না করে আমরা যদি নানারকম অভ্যন্তরীণ সংস্কারে মন দেই তাহলে সেইসব সংস্কারের সফলতা নিয়ে সেসব জাতি লাভবান হবে, যারা আমাদের দেশকে তাদের উপনিবেশ হিসাবে শোষণ করতে চায়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে যা-ই উদ্ধৃত্ত হবে, যতই দেশের সম্পদ বাড়বে ততই তাদের হাত শক্ত হবে।
এক্ষেত্রে জার্মানির কোন সাংস্কৃতিক উন্নতি বা অগ্রগতি সম্ভব নয়। কারণ যে কোন দেশের সংস্কৃতির মান রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও জাতীয় মর্যাদার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।
তাই ১৯১৯ সালের প্রথম দিকে আমরা একথা বেশ বুঝতে পারি যে দেশের জনগণকে ব্যাপক জাতীয়করণ অর্থাৎ তাদের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগানোই হবে আমাদের আন্দোলনের প্রধানতম লক্ষ্য। অবশ্য এ কাজের জন্য কতগুলি দায়-দায়িত্ব আমাদের সাধন করতে হবে। যেমন :
(১) জনগণের মনকে জাতীয় ভাবাপন্ন করে তোলার জন্য যে সামাজিক ত্যাগের প্রয়োজন তার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। জাতীয় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিপতি ও মালিকশ্রেণীর পক্ষ থেকে শ্রমিকশ্রেণীকে যতদূর সম্ভব সুযোগসুবিধা দিতে হবে। কারণ এসব সুযোগসুবিধা জনগণকে জাতীয় বৃত্তের গণ্ডীর ভেতরে টেনে আনবে। শ্রমিকশ্রেণী তাহলে জাতীয় ভাবধারায় ভাবিত হয়ে উঠবে। দেশের মধ্যে রাজনৈতিক স্থিরতা বা শৃঙ্খলা না থাকলে মালিকপক্ষের আর্থিক বা ব্যবসাগত লাভের কোন অর্থ হবে না। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় আমাদের ট্রেড ইউনিয়ন সংস্থাগুলি যদি শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য মালিকদের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে সংগ্রাম করতে এবং মালিকপক্ষকে শ্রমিকদের বেতন ও সুযোগ-সুবিধা দিতে বাধ্য করত তাহলে যুদ্ধে আমাদের পরাজয় ঘটত না। এসব আর্থিক সুযোগ-সুবিধে দিয়ে শ্রমিকদের মনকে দেশ ও জাতির প্রতি অনুগত করে তোলা যেত জাতীয় অর্থনৈতিক মূল কাঠামোর কোন ক্ষতি না করে যতদূর সম্ভব দেশের মালিকপক্ষকে লাভ কম করে আর্থিক ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকতে হবে।
(২) জাতীয় ভাবধারার দিকে লক্ষ্য রেখে জনগণকে শিক্ষাদানের জন্য পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে। তাদের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করতে হবে যাতে করে জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে এরা অংশগ্রহণ করতে পারে।
(৩) এ বিষয়ে কোন কুণ্ঠা বা দ্বিধা থাকলে বলবো সব দ্বিধা কুণ্ঠা ঝেড়ে ফেলে জনসাধারণকে প্রকৃত অর্থে মনে প্রাণে জাতীয়তাবাদী করে তুলতে হবে। এ বিষয়ে তাদের মনকে উগ্র করে তুলতে হবে। তথাকথিত ক্ষতিকারক আন্তর্জাতিকতাবাদের বিষক্রিয়াকে নষ্ট ও ব্যর্থ হলে জাতীয়তাবাদের পাল্টা বিষ প্রয়োগ করা প্রয়োজন।
কোন জাতির বৃহত্তর জনসাধারণ শুধু অধ্যাপক ও রাজনীতিবিদদের দ্বারা গঠিত নয়। এ সাধারণ জনগণ কোন জটিল ভাবধারা বা তত্ত্বের সঙ্গে মোটেই পরিচিত নয়। তারা সাধারণত জ্ঞান বা যুক্তিতে নয়, আবেগ বা অনুভূতির দ্বারা পরিচালিত হয়। সেই আবেগে অনুভূতি সদর্থক হতে পারে। জগতে আজ পর্যন্ত যত বড় বড় পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে তার মূলে কোন ভক্তি ভালবাসা বা প্রবল ঘৃণা প্রভৃতি কোন না কোন মৌল অনুভূতি বা আবেগ মূল প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে। জনসাধারণের মন জয় করতে হলে তাদের অন্তরের চাবিকাঠি লাভ করতে হবে। আর সেই চাবিকাঠি হল দৃঢ় সংকল্প।
(৪) দেশের জনগণকে কোন আন্দোলনের সামিল করে তুলতে হলে তাদের মধ্যে শুধু তাদের লক্ষ্য পূরণের জন্য এক সংগ্রামশীল সমর্থক প্রকৃতি জাগিয়ে দিয়ে চলবে না, শত্রুপক্ষকে ধ্বংস করার এক নঞর্থক প্রবৃত্তিও জাগাতে হবে। যখন কোন পক্ষ এক আপোষহীন প্রচণ্ডতায় প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে, ধ্বংস করে, তখন সাধারণ মানুষ ভাবে নিশ্চয় তারা ন্যায়ের খাতিরেই এ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু যখন দেখে আক্রমণকারীদের মধ্যে কুণ্ঠা বা দ্বিধা রয়েছে, তখন তারা স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করে তাদের এ আক্রমণ ও সংগ্রামের পেছনে কোন ন্যায়সঙ্গত যুক্তি নেই। সাধারণ জনগণ প্রকৃতিরই এক অংশ বিশেষ। তারা চায় বলবানেরা জয়লাভ করুক আর দুর্বলেরা মুছে যাক ধরাপৃষ্ঠ হতে। তবে জনগণের মন জয় করতে হলে যারা তাদের মনে আন্তর্জাতিকতার বিষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে তাদের তাড়াতে হবে শেষে।
(৫) কোন জাতির উত্থান বা পতন নির্ভর করছে তার রক্তগত উপাদানের শুচিতা ও অখণ্ডতার ওপর। যে জাতি তার রক্তের এ শুচিতাকে অক্ষুণ্ণ রাখে না বা এ ব্যাপারে গুরুত্ব দেয় না সে জাতির অন্তরাত্মা খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায়, সে জাতি কখনই সংহতি লাভ করতে পারে না। কোন জাতির রক্ত দূষিত হলেই তার জাতীয় চরিত্র নষ্ট হয়ে যায়।
সুতরাং জার্মান জাতিকে আজ বাঁচতে হলে তার জাতীয় দেহ থেকে বিজাতীয় ও বৈদেশিক বীজাণুগুলোকে দূর করতে হবে। তাদের রক্তগত পবিত্রতার সমস্যাটিকে উপযুক্ত গুরুত্ব দিতে হবে।
(৬) দেশের জনগণের জাতীয়করণের অর্থ এ নয় যে যারা উপরতলায় রয়েছে তাদের নামিয়ে আনা। কাউকে কোন স্তর হতে নামিয়ে না এনে নিচুতলার লোকদের উপরতলায় নিয়ে যেতে হবে। আমাদের যুগে যারা বুর্জোয়া বলে আখ্যাত হচ্ছে, তারা নিজেদের চেষ্টাতেই স্তরে উঠে গেছে। শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রার মানকে উন্নত করতে হলে তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নতি করতে হবে। আমাদের আন্দোলনকে সফল করে তুলতে হলে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে থেকে বেশি সদস্য সংগ্রহ করতে হবে। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে থেকে একমাত্র সেইসব লোকদের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে যারা আমাদের আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ও আদর্শকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পেরেছে।
কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর লোকদের মধ্যে ব্যাপকভাবে সদস্য সংগ্রহ করার বাধা হল তাদের আন্তর্জাতিকতাবাদ। শ্রমিকশ্রেণীর লোকের মনে যে আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শ ঢুকিয়ে দিয়েছে সেই আন্তর্জাতিকতাবাদ তাদের মন থেকে দূরীভূত করে জাতীয়তাবাদ সঞ্চারিত করতে হবে।
আমাদের আন্দোলনকে সফল করে তুলতে হলে এবং জার্মান শ্রমিকশ্রেণীকে জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ করে তুলতে হলে দেশের শিল্পপতিদের বিরুদ্ধেও এক প্রচারকার্য চালাতে হবে। তাদের কতগুলি ভুল ভাঙাতে হবে। শিল্পপতিদের মধ্যে সাধারণত এ ধারণা প্রচলিত আছে যে মালিকদের কাছে শ্রমিকদের সবসময় নত হয়ে চলতে হবে। শ্রমিকদের সব অর্থনৈতিক অধিকার ছিনিয়ে নিতে হবে। সব সুযোগ সুবিধার দাবি ত্যাগ করতে হবে, এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। শিল্পপতিদের আর একটি ভুল ধারণা হল এ যে শ্রমিকরা তাদের দাবি আদায়ের জন্য যতই তৎপর ও সংগ্রামশীল হয়ে ওঠে, ততই তারা সাধারণ মানুষের স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে।
অবশ্য একথা ঠিক শ্রমিকেরা যদি কোন অলৌকিক দাবি উত্থাপন করে অথবা অসম্ভব কিছু চেয়ে বসে তবে তারা জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধাচারণ করে। তখন তারা জাতীয় অর্থনীতির ভিত্তিটাকেই ধ্বংস করে দিতে চায়। কিন্তু শিল্পপতি ও মালিক পক্ষকেও একথা মনে রাখতে হবে যে তারা যদি শ্রমিকদের শোষণ করার জন্য কোন অমানবিক পদ্ধতি গ্রহণ করে, যদি শ্রমিকদের ন্যায্য সুযোগ সুবিধা না দেয়, তাহলে তারা জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধাচারণ করে। সেক্ষেত্রে তাকে কোন ক্রমেই জাতীয়তাবাদী বলা যায় না, কারণ তখন কেউ জাতির দেহে অনৈক্য ও অসন্তোষের বীজ বপন করে।
বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যদি এমন কোন লোক থাকে যারা মনেপ্রাণে জাতীয়তাবাদী এবং দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর দায়িত্ব যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম, তাদের অবশ্যই আমাদের সংগঠনের সদস্য করে নিতে হবে। কিন্তু বুর্জোয়ারা যদি তাদের প্রথাগত শ্রেণীচরিত্র না বদলায় তাহলে কোন মতেই তাদের মধ্যে থেকে কোন সদস্য নেওয়া চলবে না। বুর্জোয়াদের সামাজিক অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি অবশ্যই পাল্টাতে হবে।
মোট কথা আমরা কোনক্রমেই আমাদের জাতীয়তাবাদী নীতি বা কর্মপদ্ধতির কোন পরিবর্তন করব না; বরং যারা অ-জাতীয়তাবাদী বা জাতীয়তাবাদী বিরোধী তাদের যথাসম্ভব দলে টানার চেষ্টা করব। অবশ্য আমাদের আন্দোলন ও মিছিল বুর্জোয়াদের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করবে এবং তাদের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটাবে।
(৭) প্রচার আন্দোলনের এক বিশেষ অঙ্গ। কিন্তু প্রচারকার্যকে ফলপ্রদ করে তুলতে হলে দেখতে হবে প্রচার যেন সবসময় একমুখী হয়। যখন যেখানে কোন প্রচারমূলক বক্তৃতা দেওয়া হবে তখন দেখতে হবে সে বক্তৃতা যেন শ্রমিকশ্রেণী অথবা বুদ্ধিজীবীকে লক্ষ্য করে দেওয়া হয়। কারণ যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে বুদ্ধিজীবীদের সামনে বক্তৃতা দেওয়া হয়, তা’ শ্রমিকশ্রেণীর লোকেরা বুঝতে পারবে না। আবার যে ভাষায় শ্রমিকশ্রেণীর লোকেদের সামনে বক্তৃতা দেওয়া হবে তা বুদ্ধিজীবীরা পছন্দ করবে না। দেশের মধ্যে এমন বাগ্মী খুব কমই আছে যিনি আজ মেথর, কামার, মিস্ত্রী প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের কাছে সাফল্যের সঙ্গে বক্তৃতা দেবার পর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রদের সামনে অনুরূপ সাফল্যের সঙ্গে বক্তৃতা দিতে পারবেন। এখানে কোন নতুন ভাবাদর্শ সৃষ্টি বা বিশ্লেষণের কোন প্রয়োজন নেই। এখানে দরকার হল প্রকল্পিত ভাবধারাটি সাধারণ মানুষের মনে সহজভাবে তুলে ধরা।
সামাজিক গণতন্ত্র মার্কসবাদী আন্দোলন বা আদর্শ প্রভৃতি কথাগুলো শ্রমিকদের সহজেই আকর্ষণ করে। কারণ কম বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা সহজেই এসব কথা বুঝতে পারে। এবং যাদের কাছে এসব কথা বলা হয় তারা সবাই একই মনোভাবাপন্ন।
বক্তৃতার প্রকাশভঙ্গি এমন হতে হবে যা সহজেই সাধারণ জনগণের বুদ্ধির স্তরে পৌঁছতে পারে। যে বিরাট জনসভায় সাধারণ জনগণ সমবেত হয়, সেখানে এমন বক্তার দরকার যিনি জনগণের হৃদয় জয় করতে পারেন। সে সভায় উপস্থিত যদি কোন শিক্ষিত ভদ্রলোক সে বক্তৃতা শুনে তা অপছন্দ করে তাহলে বুঝতে হবে আমাদের এ নতুন আদর্শের পক্ষে সে একেবারে অযোগ্য। যেসব শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সাধারণ জনগণের ওপর প্রভাবের পরিমাণ দেখেও অনুকূল প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এসব বক্তৃতার গুণাগুণ বিচার করে, তারাই আমাদের আন্দোলনের পক্ষে উপযুক্ত ব্যক্তি। আমাদের বক্তৃতার উদ্দেশ্য যারা জাতীয়তাবাদী নয় তাদের জাতীয়তাবাদী করে তোলা। যারা এমনিতেই জাতীয়তাবাদী তাদের জন্য এ বক্তৃতা নয়।
‘যুদ্ধপ্রচার’ এ অধ্যায়ে আমি প্রচারের নীতি ও নিয়মকানুনগুলি এবং ভঙ্গিমা কী হবে তা নিয়ে আলোচনা করেছি বিশদভাবে। সেগুলির সাফল্য এ কথাই প্রমাণ করে যে সেগুলো ঠিক।
(৮) কিন্তু জনগণকে কোন বিষয়ে শিক্ষিত ও দীক্ষিত করে ভোলাই কোন রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য নয়। যে সব ভাবধারা জগতে পরিবর্তন আনতে চায়, সেই সব ভাবধারার বাস্তব রূপায়ণের জন্য এক সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতিরও প্রয়োজন হয়। কোন সামরিক অভ্যুত্থান বা কোনভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল কখনই এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য নয়। এ আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য হল জনগণের স্বার্থরক্ষা করা এবং তাদের সর্বতভাবে জাতীয়তাবাদী করে তোলা।
(৯) আমাদের নব আন্দোলনের অন্তনিহিত গঠন প্রকৃতি হল অ-সংসদীয়। যে সব সাংগঠনিক নীতির বলে সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ জোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহীত এবং নেতারা সাধারণের জীবনে এটা রূপায়িত করে তোলে মাত্র, সেই সব নীতি আমাদের এখানে প্রত্যাখ্যাত। আমাদের সাংগঠনিক নীতি হল ছোটবড় যে কোন সমস্যার ক্ষেত্রে মাত্র একজন পূর্ণ প্রভূত্ব সহকারে সকল দায়িত্ব পালন করবে।
আমাদের এ নীতির সুফলগুলি হল নিম্নরূপ :
কোন এক দলের প্রধানই সে দলের একজন সভাপতি নিযুক্ত করে। তখন সেই সভাপতিই দলের পক্ষ থেকে সব দায়দায়িত্ব পালন করে। তখন অন্যান্য সব কমিটিগুলোকে সেই সভাপতির নির্দেশ মেনে চলতে হয়। কমিটিগুলির একমাত্র কাজ হল ভোট দেওয়া নয়, সভাপতির নির্দেশ মত কাজ করে যাওয়া। প্রধান প্রধান শহর বা গ্রামদেশে কমিটিগুলো একইভাবে কাজ করে যায়। শুধু এক সাধারণ নির্বাচনে সমস্ত সদস্যদের দ্বারা দলনেতা নির্বাচিত হয়। তখন তারই আদেশে ও নির্দেশে কমিটিগুলো কাজ করে। যদি কোন সময় দেখা যায় দলের সর্বপ্রধান নেতা পার্টিবিরোধী কাজ করে চলেছে তাহলে নতুন এক সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে এক নতুন দলনেতা নির্বাচন করা হয়।
এ নীতি শুধু দলের ক্ষেত্রে নয়, সমগ্র রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যে ব্যক্তি তার নিজের সব কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করার সাহস দেখাতে পারে না, সেই ব্যক্তি নেতা হবার উপযুক্ত নয়। মানবজাতির অগ্রগতি ও সংস্কৃতি কখনো সাধারণ মানুষের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না। তা হল একান্তভাবে ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও প্রতিভার কাজ।
এ কারণেই আমাদের আন্দোলন সংসদীয় গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে। যদি কেউ সংসদীয় ব্যবস্থায় যোগদান করে তাহলে বুঝতে হবে সে আমাদের আন্দোলনকে ধ্বংস করতে চায়।
আমাদের আন্দোলন একমাত্র রাজনৈতিক সমস্যা ছাড়া অন্য কোন সমস্যার হস্তক্ষেপ করে না। এ আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য দেশের রাজনৈতিক পুনর্গঠন, ধর্মসংস্কার নয়। সুতরাং সেই সব দল এ আন্দোলনের চোখে শুক্র, যারা যে জাতীয়তাবোধ সকল ধর্ম ও নীতির ভিত্তিভূমি সেই জাতীয়তাবোধকে ধ্বংস করতে চায়।
কোন এক বিশেষ ধরনের রাষ্ট্রগঠন আমাদের আন্দোলনের উদ্দেশ্য নয়, যে সব মৌল নীতি রাজতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র যে কোন ধরনের রাষ্ট্রে ভিত্তিস্বরূপ এবং যেগুলোকে বাদ দিলে কোন রাষ্ট্রই তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে পারে না, সেই সব নীতিগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করাই এ আন্দোলনের কাজ।
কোন রাষ্ট্রের চূড়ান্ত গঠন কি হবে, তার আকৃতি ও প্রকৃতি কি রকম হবে তা সমসাময়িক যুদ্ধের প্রয়োজন অনুসারে নির্ণীত হবে। যখন কোন জাতি তার অন্তনিহিত অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত মূল সমস্যাটিকে বুঝতে পারে, তখন বাইরের কোন সমস্যাই সে জাতির মধ্যে ভাঙন ধরাতে পারে না।
(১১) সংগঠনই আমাদের আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। এটা এক কৌশলগত ব্যবস্থা মাত্র। সংগঠন লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায়মাত্র। যে সংগঠন দলনেতা এবং অনেক সাধারণ সদস্যদের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে, সেই সংগঠন মোটেই ভাল বা আদর্শ নয়। আদর্শ সংগঠনের কাজ হল দলনেতার মনে যেসব সৃষ্টিশীল ভাবাদর্শের উদ্ভব হয় সেই সব আদর্শ শুধু দলের সাধারণ সদস্যদের মধ্যে, সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া।
তবে দলের সদস্য ও সমর্থকের সংখ্যা যতই বাড়তে থাকে ততই দলনেতার মধ্যে সাধারণ সদস্যের যোগাযোগ অসম্ভব হয়ে ওঠে। তখন এজন্য দলনেতা ও সাধারণ সদস্যদের মাঝখানে এক মধ্যবর্তী সংস্থা গড়ে তোলা হয় যা নেতার সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দেয়। দলের সদস্য সংখ্যা অত্যধিক বেড়ে গেলে এক একটি স্থানে আঞ্চলিক পর্যায়ে এক একটি কমিটি গঠন করা হয়। এভাবে অঞ্চল ও জেলা কমিটির উচ্চ পর্যায়ের কর্মীদের মাধ্যমে প্রয়োজন মত কোন সাধারণ সদস্য ও দলনেতার মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা করে দেয়।
এ সব কিছু বিবেচনা করে দলের অন্তবর্তী সংগঠনের জন্য নিম্নলিখিত নীতিগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে :
(ক) দলের সমস্ত কাজকর্মের মূল কেন্দ্র হবে মিউনিক। একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য কর্মীকে প্রশিক্ষণ দান করতে হবে এবং এজন্য এক প্রশিক্ষণকেন্দ্র খুলতে হবে। দলের সুনাম অর্জন করতে হলে জনগণকে বোঝাতে হবে মার্কসবাদী নীতিই সব নয়; অন্য পাল্টা বিকল্প নীতিও সম্ভব।
(খ) মিউনিকে কেন্দ্রীয় কমিটির প্রভুত্ব ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত কিন্তু কোন আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা চলবে না।
(গ) জেলা, আঞ্চলিক ও প্রাদেশিক পর্যায়ে কমিটিগুলি একমাত্র তখনি গঠন করা হবে যখন এগুলোর একান্ত প্রয়োজন দেখা দেবে এবং কেন্দ্রীয় কমিটি সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।
তাছাড়া স্থানীয় কমিটি গঠনের সময় দেখতে হবে সেই সব সংগঠনের পরিচালনার ভার গ্রহণ করার উপযুক্ত নেতা পাওয়া যাচ্ছে কিনা। এর সমাধানের দুটো পথ আছে :
(ক) প্রথম উপযুক্ত পরিমাণ টাকার জোগাড় করতে হবে। সেই টাকা দিয়ে যোগ্য বুদ্ধিমান লোক বেছে নিয়ে তাকে প্রশিক্ষণ দান করতে হবে। এভাবে বেতনভোগী যোগ্য লোক নিযুক্ত করলে সে ঠিক অবস্থা বুঝে কাজ করে যাবে।
(খ) এ কাজ সহজ হলেও বহু টাকার প্রয়োজন। প্রথম প্রথম অবৈতনিক লোকের ওপরে নির্ভর করতে হবে। আন্দোলনের নেতারা তাই এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে এমন এক উদার সদাশয় ব্যক্তির খোঁজ করবে যারা আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য দলকে সাহায্য করবে। দরকার হলে অর্থ সাহায্যও করবে।
উপযুক্ত নেতা যে অঞ্চলে পাওয়া যাবে না, সেখানে কোন মতেই কোন স্থানীয় বা আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা যাবে না। কোন সেবাদল যেমন উপযুক্ত অফিসার ছাড়া চলতে পারে না, তেমনি কোন রাজনৈতিক দল উপযুক্ত নেতা ছাড়া চলতে পারে না।
নেতা হবার প্রবল বাসনাই কোন নেতার একমাত্র গুণ নয়। সঙ্গে চাই ইচ্ছাশক্তি আর উদ্যম। প্রতিভা, সংকল্প আর অধ্যবসায়, এ তিনটি গুণের সমন্বয় যেকোন নেতার চরিত্রে একান্ত দরকার।
(১২) আন্দোলনের ভবিষ্যত নির্ভর করে দলের সদস্যদের আদর্শ, নিষ্ঠা, একাগ্রতা এবং উদ্যমের ওপর। তাদের এটা সব সময় ভাবতে হবে যে তারা ন্যায়সঙ্গত কারণেই লড়াই করছে।
অনেকে মনে করে একটি আন্দোলন অনুরূপ ধরনের আর একটি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করতে পারে। কিন্তু তাতে আন্দোলনের আয়তনটা বাড়তে পারে লোকচক্ষে। গুণগত মান তাতে বাড়বে না। বরং তার সাংগঠনিক শক্তি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কোন আন্দোলন তখনই বড় হতে পারে যখন তার অন্তনিহিত শক্তিটি অব্যাহতভাবে বেড়ে যায় এবং অন্যান্য প্রতিযোগীদের ছাড়িয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।
সুতরাং আমরা নিরাপদে এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে কোন আন্দোলনের উন্নতির জন্য সংগ্রাম দরকার। এবং কঠোর সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে অর্জিত শক্তিই কোন আন্দোলনের চূড়ান্ত সাফল্য দান করতে পারে। কোন আন্দোলন কখনো ক্ষণস্থায়ী বা মোটামুটি ধরনের জয় বা সাফল্য কামনা করে না। প্রতিটি আন্দোলনের লক্ষ্য হবে দীর্ঘ সগ্রামের মধ্য দিয়ে এক স্থায়ী জয়ের গৌরব লাভ করা। একটি আন্দোলনের সঙ্গে অন্য একটি আন্দোলনকে যুক্ত করা আর একটি চারাগাছকে গবেষণাগারে রেখে কৃত্রিমভাবে বাড়ানো একই কথা। কৃত্রিমভাবে বাড়ানো এ গাছ কখনই স্বাভাবিক গাছের মত সেই অন্তনিহিত শক্তি অর্জন করতে পারে না, যে শক্তির জোরে কোন স্বাভাবিক গাছ যুগ যুগ ধরে সমস্ত ঝড় ঝঞার প্রকোপকে সহ্য করতে পারে।
(১৩) আন্দোলনের কর্মকর্তারা দলের সদস্যদের এ শিক্ষাই দেবে যে যুদ্ধ মানেই অভিশাপ বা কোন অশুভ শক্তি নয়। তাদের অস্তিত্বকে সুদূর এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে যুদ্ধের প্রয়োজন আছে। সুতরাং শত্রুদের শক্রতার ভয়ে তারা ভীত হবে না; বরং সেই শক্রতাকে বরণ করে নিয়ে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে তারা জয়ের পথে এগিয়ে যাবে।
আন্দোলনকারীদের সব সময় একথা মনে রাখতে হবে যে ইহুদীদের পত্রিকাগুলো তাদের বিরুদ্ধে সর্বদা মিথ্যা ও কুৎসা রটনা করে যাবে। মিথ্যাবাদী ইহুদীদের একমাত্র। অস্ত্রই হল মিথ্যা আর ছলনা।
(১৪) ব্যক্তিগত প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের প্রতি যাতে উপযুক্ত শ্রদ্ধা দেখানো হয়, তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাবে আমাদের আন্দোলন। মানবিক মূল্য বলতে যা বোঝায় তা হল ব্যক্তিগত সৃষ্টিশীল শক্তির ফল। শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সামরিক শক্তি ও বীরত্ব প্রভৃতি বিষয়ে যারা যশ অর্জন করেছে তাদের কোন বিকল্প নেই। কোন বিখ্যাত শিল্পী একটি ছবি আঁকতে তাঁর আরদ্ধ কাজ ফেলে রাখলে সে কাজ তার কোন শিষ্য বা ছাত্র তা শেষ করতে পারে না। পৃথিবীর বড় বিপ্লব, সবচেয়ে বড় সাংস্কৃতিক উন্নতি, রাজনীতিবিদদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি, মানুষের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব সব একক মানুষের অবদান।
ইহুদীরাও এটা ভালভাবে জানে; তাদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি তারাই যারা মানবজাতি ও মানব সভ্যতা ধ্বংস করতে পারদর্শী।
মানুষের অন্তরাত্মা যখন মাঝে মাঝে নিবিড়তম হতাশায় ভেঙে পড়ে, যখন মানুষের মন সামনের দিকে এগিয়ে চলার কথা ভুলে গিয়ে অতীতের ছায়ার আশ্রয় নেয়, তখন এক একজন প্রতিভাধর পুরুষ এসে তাদের মনে অফুরন্ত উৎসাহ সঞ্চার করে তাদের পিছিয়ে যাওয়া মনকে আবার অগ্রগতির পথে ঠেলে দেয়।
আমাদের কেউ চিনত না। আমাদের এ আন্দোলনের ভবিষ্যত উজ্জ্বল এ বিশ্বাসকে আমরা ধর্মবিশ্বাসের মত আঁকড়ে ধরে থাকতাম। কিন্তু তখন আমাদের পার্টি মিটিংয়ে মোটেই লোক হত না। আমি যখন এ পার্টিতে ভর্তি হই, তখন আমাদের পার্টি মিটিংয়ে মোটে সাত আটজন লোক যোগদান করত।
এরপর আমরা ঠিক করি প্রতি মাসে একটা করে আমরা সাধারণ সভা করব। সেই সভার জন্য আমরা টাইপ করে ও হাতে লিখে অনেক নিমন্ত্রণপত্র ছড়ালাম। যে যার পরিচিত লোকদের সঙ্গে দেখা করে অনেক নিমন্ত্রণপত্র বিলি করা হল। কিন্তু এত কিছু করা সত্ত্বেও সেই সাতজনের বেশি একজনও এলো না।
এরপর টাইপ করে আরো নিমন্ত্রণপত্র ছড়ালাম। লোকসংখ্যা বাড়তে বাড়তে তিরিশে গিয়ে দাঁড়াল। এরপর আমরা ‘মিউনিক অবজারভার’ নামে এক নিরপেক্ষ পত্রিকায় আমাদের মাসিক সভার জন্য বিজ্ঞাপন দিলাম। মিউনিকের এক বড় হল ঘরে সভা হল। দেখা গেল একশো এগারো জন লোক সেই সভায় যোগদান করেছে। একজন অধ্যাপক প্রথমেই সেই সভায় বক্তৃতা করলেন। আমাকে বক্তৃতা দেবার জন্য সভাপতি মাত্র কুড়ি মিনিট সময় দিয়েছিল। আমি মোট তিরিশ মিনিট বক্তৃতা করলাম। জীবনে আমার সেই প্রথম বক্তৃতাতেই আমি অপ্রত্যাশিত ভাবে সাফল্য লাভ করেছিলাম। শ্রোতাদের মনে আমার বক্তৃতা গভীরভাবে রেখাপাত করে। দর্শকদের কাছে চাঁদা বা অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন জানাতে সঙ্গে সঙ্গে আমরা তিনশো মার্ক লাভ করি। তাতে আমরা পার্টি ফাণ্ড গড়ে তুলি। অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে পার্টির জন্য পুস্তিকা ছাপা ও সেগুলো বিলি করার ব্যবস্থা করি।
এ সভার সাফল্যের ফলে আমরা বেশ কিছু লোককে আমাদের দলে সদস্য হিসেবে পেয়েছিলাম। এ সময় সাধারণ মানুষকে আবেগময় ভাষায় বোঝাবার মত লোক ছিল না আমাদের পার্টিতে। আমাদের দলে যে অধ্যাপক ভদ্রলোক ছিলেন তিনি সাধারণ মানুষের সামনে ভাল বক্তৃতা দিতে পারতেন না। অবশেষে সে ভার আমাদের কাঁধের ওপর এসে পড়ে।
কিন্তু তখন আমাদের সভার সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল কমিউনিস্টরা। প্রথম প্রথম কমিউনিস্টরা আমাদের সভাকে বুর্জোয়াদের সভা বলে গ্রাহ্য করত না। পরে আমাদের সভার ক্রমবর্ধমান সাফল্য দেখে আমাদের সভা বসতে বসতেই তা ভেঙে দেবার চেষ্টা করত।
প্রথম প্রথম তাদের দেখলেই আমাদের সভার দর্শকেরা পালিয়ে যেত। তারা কিছু করলেও ভয় পেত। পরে দেখা গেল তারা আমাদের সভাতে কোনরকম যোগদান করতে এলেই আমাদের সভার দর্শকরাই তাদের প্রতিহত করত সঙ্গে সঙ্গে।
আমাদের সভায় যখন একশো সত্তর জন লোক যোগদান করল তখন আমি আরো বড় হলে সভা করার প্রস্তাব দিলাম। আমি এক সভায় বললাম যে শহরে সাত লক্ষ লোক বাস করে, সেখানে সপ্তাহে একটা করে সভা করা যায়। আমাদের আত্মবিশ্বাস নিয়ে আমাদের পথের সামনে পর্বতপ্রমাণ বাধা বিপত্তি সব পুড়িয়ে ছারখার করে দিতে পারব।
সভার লোকসংখ্যা ক্রমশই বাড়তে লাগল। দুশো থেকে সেই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল বারশোতে। মাত্র পনেরো দিনের ব্যবধানে এ সংখ্যা বেড়ে যায়। এ সময় আমাদের আন্দোলন তার অন্তর্নিহিত শক্তির জোরে উদ্দাম হয়ে ওঠে। তবে এ সময় কিছু লোক আমাদের আন্দোলনকে এক রাজনৈতিক দল বলে অভিহিত করতে থাকে। আমি বুঝলাম একথা সেই সংকীর্ণমনা সমালোচকের দল বলছে যারা কোন আন্দোলনের বহিরঙ্গের শক্তি আর তার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির মধ্যে কোন পার্থক্য করতে পারে না। এটা তাদের বোঝানো কঠিন হয়ে উঠল যে কোন আন্দোলন যতদিন না তার আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে সফল করে তুলতে পারে ততদিন তা পার্টি হিসেবেই কাজ করে। যখন কোন লোক জনগণের মঙ্গলের কোন মৌলিক আদর্শকে রূপায়িত করে তুলতে চায়, তখন সে তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কিছু সমর্থক ও ভাবশিষ্যের সন্ধান করে। তখন সেই আদর্শের স্রষ্টা এবং নেতা তার সমর্থক ও শিষ্যদের কর্মপ্রচেষ্টা একটি পার্টির রূপ নেয়। কিন্তু পার্টি সংগঠন তাদের মূল লক্ষ্য নয়, তাদের মূল উদ্দেশ্য হল আদর্শের রূপায়ণ। তাদের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য সফল না হওয়া পর্যন্ত এ পার্টির উদ্দেশ্য বজায় থাকবে। কিন্তু মানুষ তাদের অতীতের সংকীর্ণ অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে কার্য তৎপরতাকে পার্টির নাম দেয়।
এ সময় আমি আমার সমর্থকদের আর একটা বিষয়ে সতর্ক করে দেই। যাতে বাজে কোন লোক আমাদের দলে ঢুকে পড়ে আন্দোলনকে বানচাল করে দিতে না পারে তার জন্য সে বিষয়ে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। আমি বলি এমন কিছু লোক আসবে যাদের আসলে কোন যোগ্যতা নেই অথচ যারা মুখে বলে বেড়াবে তারা চল্লিশ বছর ধরে এ একই আদর্শ রূপায়ণের জন্য চেষ্টা করে আসছে, সংগ্রাম করে আসছে। আমার বক্তব্য যদি কোন লোক চল্লিশ বছরে চেষ্টা করেও কাজ সফল করে তুলতে না পারে, তাহলে বুঝতে হবে সে লোক সেই কাজে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। কোন লোক চল্লিশ বছর ধরে এক খামার বানিয়ে যদি সে খামারের উন্নতি সাধন করতে না পারে, ভাল ফসল ফলাতে অক্ষম হয়, তাহলে বুঝতে হবে সে লোক অযোগ্য। এ ধরনের লোকের কোন প্রয়োজন নেই আমাদের। তবে অবশ্য তাদের মধ্যে খুব কম লোকই নিঃস্বার্থভাবে নতুন আন্দোলনে যোগ দিয়ে কাজ করতে আসবে। তারা শুধু অতীতের অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে বর্তমানের সব সমস্যার সমাধান করতে চায়। আসলে তারা ভীরু, মুখে বীরত্বের ভাণ করলেও কার্যক্ষেত্রে ভয়ে পালিয়ে যায়।
কিন্তু যেসব ইহুদী এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করতে চায় তাদের কাছে ঐসব হাসির নায়কদের দাম আছে। তারা কিছু না জেনেও সব জানার ভাণ করে। এসব তথাকথিত নায়কদের মধ্যে আবার দু’শ্রেণীর লোক আছে। একজন অলস অকর্মণ্য, তারা কিছুই করতে চায় না। তাদের কোন বিশেষ উদ্দেশ্য বা আদর্শ নেই। কিন্তু আর একজনের এক বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। তারা ধর্মসংস্কারের নামে রাজনৈতিক আন্দোলনের সব কর্মতৎপরতা ও সংগ্রামকে ব্যর্থ করে দিতে চায়। তাদের কাছে জাতীয়তাবাদের কোন মূল্য নেই। জাতীয়তাবাদের আদর্শের পতাকাতলে সমবেত ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে জার্মানির জনগণ লড়াই করে যাবে একটা তারা চায় না!
আমরা এসব লোককে বলতাম জনতা। আমরা দলের মধ্যে এ জনতার অনুপ্রবেশ একেবারে বন্ধ করার জন্য আমাদের দলের নামকরণ করলাম ন্যাশনালিস্ট সোশ্যালিস্ট জার্মান লেবার পার্টি।
আমাদের দলের এ নামকরণ শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাচালের দল পেছনে লাগল। কুৎসা রটনা করতে লাগল। কিন্তু তাদের ভয় পাবার কিছু নেই। কারণ তাদের যা কিছু লড়াই তা শুধু কথার। আমরা আমাদের শত্রুদের সতর্ক করে প্রকাশ্য ঘোষণা করি আমাদের ওপরে যারা জোর করতে আসবে, আমরাও তাদের ওপর জোর করব।
আর এক ধরনের শক্রর সম্পর্কেও আমি সাবধান করে দিলাম আমাদের দলের লোকদের। একদল লোক আছে যারা নিজেদের নীরব কর্মী বলে প্রচার করার চেষ্টা করে, অথচ আদতে তারা অলস অপদার্থ। তারা নিজেরা কাজ না করে শুধু অপরের কাজের সমালোচনা করে। যারা কাজের লোক তাদের নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করে। আমাদের জাতীয় পুনর্গঠনের কাজকে তরান্বিত করতে হলে এসব ভদ্র তথাকথিত নীরব কর্মীদের সম্পর্কে সব সময়ে সচেতন থাকতে হবে।
১৯২০ সালের প্রথমদিকে আমি এক প্রকাশ্য বিরাট জনসভা আহ্বান করার কথা বলি। বামপন্থী সংবাদপত্রগুলো আমাদের বিরুদ্ধে প্রচার চালাতে লাগল আমি বলি যে এটা ভাল লক্ষণ। আমাদের বিরোধীপক্ষরা যত আমাদের সঙ্গে পারছে না, ততই আমাদের নাম প্রকারান্তরে প্রচারিত হচ্ছে। জনসাধারণ আমাদের দলের নামের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠছে। এতে আমাদের সুবিধাই হবে।
আমি জানতাম বামপন্থী দলের লোকেরা আমাদের বাধা দেবে। আমাদের জনসভা পণ্ড করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে। কিন্তু আজ হোক বা কাল হোক এটার সম্মুখীন তো হতে হবে। এড়িয়ে গেলে চলবে না। সুতরাং জনসভার অনুষ্ঠান করতে হবেই। তাছাড়া যখন আমরা প্রথম আন্দোলনে নামি, তখন আমরা সগ্রামের মধ্যে নিজেদের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করার সংকল্পই করেছিলাম। আমাদের সভাপতি বীরের মত আমার প্রস্তাবের প্রত্যক্ষ বিরোধিতা না করে সভাপতি পদ ত্যাগ করে চলে যায়। পরবর্তী সভাপতি ডেস্কনার আমার প্রচারের কাজে কোন বাধা দেয় না। আমরা ১৯২০ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি জনসভার দিন ধার্য করি।
যেহেতু আমার ওপর প্রচারের সব ভার ছিল, আমি জনসভার জন্য আনুসঙ্গিক এবং আবশ্যকীয় সব প্রস্তুতি করতে থাকি। চারিদিকে পোস্টার দেওয়া হয়। পুস্তিকা এমনভাবে লিখি যাতে তা জনগণের মনকে সহজে আকৃষ্ট করে। এতসব করার পর আমরা এর ফল কি হয় তার প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করতে থাকি।
আমরা দলের পতাকা ও কাগজপত্রে সব ব্যাপারে লাল রঙ ব্যবহার করতে লাগলাম। তখন ব্যাভেরিয়ার ন্যাশানাল পিপলস পার্টি সরকারে প্রতিষ্ঠিত থাকলেও তাদের সঙ্গে মার্কসবাদীদের আঁতাত ছিল। তাই মার্কসবাদীদের প্ররোচনায় পুলিশ রাস্তা থেকে আমাদের অনেক প্লাকার্ড বাজে অজুহাতে সরিয়ে দিল। তবু আমরা প্রচার চালিয়ে যেতে লাগলাম। তবে ব্যাভেরিয়া সরকারের অধীনে কর্মরত পুলিশের কর্মকর্তা আর্নেষ্ট পয়গর ও ডক্টর ডিক মনেপ্রাণে জাতীয়তাবাদী ছিল।
জনসভার একমাস আগেই প্রয়োজনীয় টাকাপয়সার জোগাড় হয়ে যায়। মিউনিকের এক বিরাট হলে জনসভা অনুষ্ঠিত হল। সভার কিছুক্ষণ আগে আমি গিয়ে দেখি সমস্ত হল লোকের ভিড়ে ভরে গেছে। প্রায় ছ’হাজার লোক সভায় যোগদান করেছে। সভায় প্রথম বক্তার পর আমি বক্তৃতা দিতে উঠতেই এক বাধার সম্মুখীন হই। সভার একদিকে একজন লোক ঝটিতি উঠে এসে বারে বারে আমার বক্তৃতায় বাধা দিতে থাকে। কিন্তু সভার লোক তার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে তাকে হল থেকে বার করে দেয়। আমি বক্তৃতা দিতে থাকি আবেগের সঙ্গে। আমার আবেগময় বক্তৃতা এক উত্তপ্ত উত্তেজনার মধ্যে শ্রোতারা শুনতে লাগল। মনে হল তারা যেন নতুন বিশ্বাস খুঁজে পেয়েছে। এক কঠিন সংকল্প ফুটে উঠেছে তাদের মুখে।
চার ঘণ্টা পর উল্লসিত জনতা যখন সভাগৃহ ছেড়ে যেতে লাগল তখন আমি বেশ বুঝতে পারলাম জার্মানিতে এক বিপ্লব সংগঠিত হতে চলেছে।
বুঝতে পারলাম বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছে। সে আগুনের আঁচে সেই সগ্রামের অস্ত্রগুলো শাণিত হচ্ছে, যে সংগ্রাম নবজীবন আনবে সমগ্র জার্মান জাতির মধ্যে। বুঝলাম প্রতিহিংসার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ১৯১৮ সালের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিতে চলেছে।
দেখতে দেখতে হলঘর শূন্য হয়ে গেল। তবু মনে হল বিপ্লবের অদৃশ্য রথ জয়যাত্রার পথে এগিয়ে চলেছে।