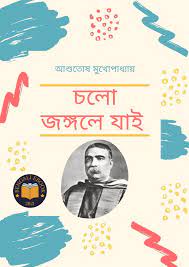- বইয়ের নামঃ চলো জঙ্গলে যাই
- লেখকের নামঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
- বিভাগসমূহঃ গল্পের বই
আশা আর বাসা
ছিল পোস্টমাস্টারের মেয়ে। নিজে কিছুকাল করল স্কুল-মাস্টারি। তারপর হয়ে পড়ল কলেজের মাস্টারের বউ।
জীবনের এই কোনো ক্ষেত্রই পছন্দ নয়। পোস্টমাস্টার বা স্কুল-মাস্টার অথবা কলেজের মাস্টার যে তার চক্ষুশূল এমন নয়, বরং পোস্টমাস্টার বাবাটিকে সে ভালই বাসত, তার সদা খুঁতখুঁতে মনোভাব দেখে বেশ মজা পেত। ড্রয়ারে একটা কাগজ রাখলেও তিনবার করে খুলে দেখতেন ঠিক রেখেছেন কিনা। কারো হাতে একটা দশ টাকার নোট দিলে দুতিনবার অন্তত সেটা টেনে নিয়ে আঙ্গুলে ঘষে দেখতেন একটার জায়গায় দুটো বেরিয়ে গেল কিনা।
নিজে যতদিন স্কুল-মাস্টারি করেছে ততদিন খুব যে নিরানন্দে ছিল তাও নয়। বরং সমবয়সী সতীর্থদের সঙ্গে হেসে-খেলে দিন কাটিয়েছে। তাদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছে।
আর কলেজের মাস্টারের বড় হবার জন্যেও কেউ তাকে বাধ্য করে নি। নিজের ইচ্ছেতেই হয়েছে। ঘরে প্রায় সর্বদাই পাঠ আর পঠনরত অল্পবয়সী একটি সিরিয়স মুখ দেখে এক-এক সময় সে বেশ কৌতুকই অনুভব করত। কোন সময় বা টেনে টেনে ছড়া কাটত, রাম গরুড়ের ছানা হাসতে তাদের মানা। ফলে ইতিহাসের তরুণ মাস্টারের অনেক সময়ই পাঠ-পঠনের মনোযোগ রসাতলে যেত। তার হাসিতে প্রমাণ মিলত হাসির রসদ পেলে তার হাসতে তেমন মানা নেই, আর রাতের নিভৃতে এই টিপ্পনীর দরুণ দস্তুরমত হামলা করে চড়ামাশুলও আদায় করতে চেষ্টা করত। তখন সমর্পণের হাল ছাড়তে খুব মন্দও লাগত না।
তবু এই তিনের একটা ক্ষেত্রও যে পছন্দ নয় তার কারণ ওর নিজের চরিত্রগত উচ্ছলতা। ওই তিনের কোন ক্ষেত্র থেকেই সেটা পরিপূর্ণ রসের জোগান পেত না। উচ্ছল সত্তা বিকশিত বা বিস্তৃত হবার মতো সেগুলির একটাও তেমন প্রশস্ত নয়, উর্বর নয়-মানিয়ে নিতে পারলে দিন এক রকম করে কাটে, এই পর্যন্ত। কিন্তু বর্ণশূন্য দিনযাপনের সহিষ্ণুতা তার কম। বরং বর্ণের অনুশীলনে সেটা কত ভাবে কত রকমে উজ্জ্বল হতে পারে সেই কল্পনার সঙ্গে তার মানসিক যোগ।
এরও কারণ আছে।
নাম রাখি। আগে গাঙ্গুলি ছিল। কলেজের মাস্টারের ঘরে এসে চক্রবর্তী হয়েছে। রাখি চক্রবর্তী। বর্ণবিলাসী কল্পনার সঙ্গে তার মানসিক যোগের কারণ বিশ্লেষণ এই নাম থেকেই শুরু করা যেতে পারে।
ওর বাবারা পাঁচ ভাই। জলপাইগুড়িতে একান্নবর্তী পরিবার। তাদের কেউ স্কুল মাস্টার, কেউ উকিল, কেউ কেরানী। বাবা পোস্টমাস্টার আর ছোট কাকার স্টেশনারি দোকান। রাখির বাবা সেজ। রাখির চারটি নিজস্ব দাদা। বড় জ্যাঠা আর মেজ জ্যাঠার চারটি করে ছেলে। বড় কাকার ছয় ছেলে। ছোট কাকার পাঁচ ছেলে। সব মিলিয়ে বাড়িতে ছেলের সংখ্যা তেইশ। আর একটি মাত্র মেয়ে–সে রাখি। মেজ জ্যাঠার নাকি একটা মেয়ে হয়েছিল। সে দেড় বছরের বেশি টেকেনি। বাড়িতে মেয়ের দুর্ভিক্ষ। সাধারণত লোকে ছেলে হলে খুশি হয়, কিন্তু এ বাড়িতে ছেলের মুখ দেখতে দেখতে এমন অবস্থা যে ছেলে হলে মন-মেজাজ খারাপ হয়। ছোট কাকিমার কাছে রাখি শুনেছে, ওর ছোড়দা যখন হল, মায়ের সে কি কান্না! কে নাকি হাত দেখে মাকে বলেছিল এবারে ছেলে হবে!
এহেন পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ আগন্তুক কন্যা। স্বভাবতই তার আদর, তার কদর, তার প্রশ্রয় অন্যরকম। ও এসেছে তাই আনন্দ ধরে না, শেষ পর্যন্ত টেকে কি টেকে না ভিতরে ভিতরে সেই শঙ্কা। সেই কারণেই নাম–রাখি। তা ছেলেবেলা থেকে সকলে মাথায় করেই রেখেছে তাকে। বৃহৎ পারিবারে অনটনের ছায়া পড়েই ছিল। কিন্তু সেটা একমাত্র ওকেই স্পর্শ করে নি কোনদিন। যখন যা চেয়েছে তাই পেয়েছে। বাবা না দিলে কাকা-জ্যাঠারা দিয়েছে। বছর পনের বয়েস পর্যন্ত অন্তত চাইলে পাবে না এমন কিছু আছে বলেই সে ভাবতে পারত না। তার চোখে তখন পর্যন্ত সমস্ত দুনিয়াটাই বর্ণে গন্ধে আনন্দে ভরা।
স্কুল ফাইন্যাল থেকে বি.এ. পাস করার চারটে বছরের মধ্যে পর পর কটা বিপর্যয়ে সেই রংদার দুনিয়ার সব বর্ণ সব গন্ধ আর সব আনন্দ যেন কর্পূরের মতো মিলিয়ে গেল চোখের সমুখ থেকে। আর যে বাস্তব মুখব্যাদান করে তার সামনে এগিয়ে এলো সেটা যেমন নীরস, তেমনি অকরুণ। পনের বছর পর্যন্ত যে মেয়েটা সব পেয়েছে, এ বাস্তবের সঙ্গে তার আপোস করে চলাটা সহজ নয়।
ওই চার বছরের গোড়ায় বড় কাকা চোখ বুজলেন। তারপর বড় জ্যাঠা। শেষে বি. এ. পাস করার ছমাস আগে তার বাবা মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের তাপ্লি মারা নৌকোটা হঠাৎ যেন খান-খান হয়ে গেল।
বি. এ. পাশ করার আগেই রাখি গাঙ্গুলি যেন অকূল পাথারে পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগল। নিজের এবং খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো তেইশটি দাদার মধ্যে মতের মিল থেকে অমিলই বেশি। অনেকেই বিয়ে-থা করেছে, অনেকেই বাইরে চাকরি-বাকরি করছে–কিন্তু পৈতৃক বাড়ির বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কে যে যার ভিন্ন-মতে মাথা ঘামাতেও কসুর করছে না। একান্নবর্তী পরিবারের জমিজমা কিছু ছিল।! চার বছরের মধ্যে সেসব শূন্যে মিলিয়ে গেল। পৈতৃক বাড়িতে যারা থাকে তাদের প্রতি যারা থাকে না তাদের যেন একধরণের অনুকম্পামিশ্রিত উদারতা। ইচ্ছে করলে ওই বাড়িও বেচে দেওয়ার দাবি তোলা যেতে পারে, ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে গেলে তো কারো ভাগেই কয়েকখানা করে ইট-কাঠের বেশি কিছু পড়বে না। অতএব বেচে দেবার দাবি না তোলাটা প্রকাশ্য উদারতা ছাড়া আর কি!
বাবা মারা যাবার কিছুদিনের মধ্যে জানা গেল ভদ্রলোক মেয়ের বিয়েবাবদ আলাদা। করে কিছু টাকা রেখে গেছেন। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা মা আর ছেলেরা পাবে। এ টাকাটা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত। আলাদা। বড়জোর হাজার পাঁচেক হবে–তাই নিয়েই আড়ালে-আবডালে কথা। যে জ্যাঠা আর কাকা মারা গেছেন, তাদের ছেলেদের সংশয়, এত খরচের মধ্যে বাবা মেয়ের জন্যে ওই টাকা জমালেন কী করে? শেষের কয়েকটা বছর এই একান্নবর্তী সংসার পরিচালনার ভার রাখির বাবার ওপরেই ছিল।
অপরের কথা দূরে থাক, একমাত্র ছোট বোনের প্রতি বাবার পক্ষপাতিত্ব দেখে। দাদারাও কেউ কেউ গম্ভীর। তার কারণ, তারা দেখেছে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকার একটা বড় অংশই বাবা ধারে কমিয়ে রেখে গেছেন। সেই কারণেই ছোট বোনের নামে পাঁচ হাজারের অঙ্কটা তাদের চোখে খুব কম ঠেকেনি।
বি. এ. পরীক্ষার মাত্র মাসতিনেক আগে বড়দার কথা শুনে তো রাখির চোখে জলই এসে গেছল। গম্ভীর মুখে বড়দা মাকে বলছিল, পরীক্ষার জন্যে আবার কতগুলো টাকা খরচ করে কী হবে, পড়াশুনায় যা মন আর যা মাথা, নির্ঘাৎ ফেল করবে আর টাকাগুলোও যাবে। তার থেকে চেষ্টা-চরিত্র করে বিয়েই দিয়ে দাও, ঝামেলা মিটে যাবে।
মা অবশ্য দাদার কথায় কান দেয়নি। আর পরীক্ষার ফীও ছোট কাকা নিজে থেকে ডেকে দিয়েছে ওকে। কিন্তু বড়দার কথা শুনে ও যত না দুঃখ পেয়েছিল তার থেকে তাজ্জব হয়েছিল ঢের বেশি। বাড়ির একটামাত্র এত আদরের মেয়ে সে। কিনা এরই মধ্যে ঝামেলার সামিল! যেমন-তেমন করে তাকে বিদায় করতে পারলে ঝামেলা মেটে!
সেই প্রথম নিজের ওপর ভয়ানক রাগ হয়েছিল রাখি গাঙ্গুলির। পড়াশুনায় তার কোনদিন খুব একটা মন ছিল না সত্যি কথা। প্রতিবার যখন পরীক্ষাসংকট একেবারে নাকের ডগায় এগিয়ে আসে তখনি প্রতিজ্ঞা করে, ঠাকুরের দয়ায় সেবারের মতো। কোনরকমে উতরে গেলে জীবনে আর পড়াশুনায় গাফিলতি করবে না। কিন্তু উতরে যাবার পর প্রতিজ্ঞার কথা আর মনে থাকে না। কিন্তু তা বলে পড়শুনা করলে পাস না করার মতো মাথাও নেই তার? বরং স্কুলে পড়তে টিচাররা উল্টো কথাই বলত। বলত, মেয়েটার মাথা ছিল, পড়াশুনা মন দিয়ে করলে ওই সোমা মিত্রর থেকেও ভালো করত। সোমা প্রতি বছর একগাদা প্রাইজ নিয়ে বাড়ি ফিরত। বি. এ.-তেও সে অনার্স পড়ছে আর আশা করছে ভালো রেজাল্ট করবে। নিজের ওপর রাখির রাগ এই জন্য, কেন এতগুলো বছর সে হেলায় হারালো, কেন সকলের জিব নাড়া বন্ধ করার মতো রেজাল্ট করল না আগাগোড়া!
যাই হোক, সাংসারিক বিপর্যয়ের পর বিশেষ করে বাবা মারা যাবার পর রাখি গাঙ্গুলি বেশ টের পাচ্ছিল সে কোন মাটিতে দাঁড়িয়ে আছে। খানিকটা নিজের ওপর আর সক্কলের ওপর রাগ করে, খানিকটা ঝোঁকের মাথায়, আর খানিকটা বা বেগতিক দেখে পরীক্ষার কটা মাস এমন পড়াই পড়ল যে শুধু পাশ নয়, ডিস্টিংশনে পাস।
পাস করার পর বাবার মৃত্যটা যেন আরো বেশি অনুভব করল সে। বাবা বেঁচে থাকলে যেমন করে যোক কলকাতায় থেকে এম. এ. পড়ার ব্যবস্থা করা যেত। উৎসাহের আতিশয্যে মনে মনে একটা হিসেব করে ফেলল সে। যে পাঁচ হাজার ঢাকা বাবা ওর নামে রেখে গেছেন তার থেকে দুবছরে হাজার আড়াই খরচা করে কলকাতার কোনো হস্টেলে থেকে এম.এ-টা পড়ে ফেললে কেমন হয়? কিন্তু মাকে এ প্রস্তাবে রাজি করানো গেল না। তার পড়াশুনার ব্যাপারে বাড়ির মধ্যে আগ্রহ ছিল। একমাত্র যে মানুষটির তিনি ছোট কাকা। তিনিও এ প্রস্তাবে সায় দিলেন না।
ফলে প্রায় একটা বছর বেকার দশা। মাঝে দুমাস একমাসের জন্য যে স্কুলে পড়ত সেই স্কুলে কাজ করেছে। কোনো টিচার ছুটিছাটায় গেলে তবে সেরকম কাজ মেলে।
ইতিমধ্যে ওর সহপাঠিনী এবং স্কুল-কলেজের ভালো মেয়ে সোমার মস্ত ঘরে বিয়ে হয়ে গেল। সোমা এমন কিছু রূপসী নয় তার থেকে। বরং স্কুল-কলেজে পড়তে করলা নদীর ধারে অথবা তিস্তার চরে ওরা দল বেঁধে হুটোপুটি করত যখন, সেদিককার ছোঁড়াগুলোও দল বেঁধে আসতই। ওর সঙ্গেই গায়ে পড়ে বেশি আলাপ করতে চেষ্টা করতে, আর পাত্তা না দেবার ফলে ওকেই বেশি জ্বালাতন করত।
কিন্তু বিয়েটা ওদের মধ্যে সোমারই সব থেকে ভালো হল। বান্ধবীদের বিয়ে আরো কারো কারো হয়েছে, কিন্তু সোমার মতো কারো নয়। সোমার বাবার টাকার জোর ছিল, অঢেল খরচ করেছেন তিনি। ছেলে আই. এ. এস অফিসার। আর সেই বিয়ের রাতে সোমাকে যেন রাজকন্যার মতো লাগছিল রাখির। সোমার পরে আরো দুই-একটি অন্তরঙ্গ বান্ধবীর বিয়ে হয়েছে। তাতেও ঘটা মন্দ হয়নি। এ-সবের মধ্যে পাঁচ হাজার টাকায় নিজের বিয়ের চিত্রটা এত অনুজ্জ্বল ঠেকেছে চোখে যে মনে হয়েছে। তার থেকে বিয়ে না হওয়াই ভালো। বান্ধবীদের কাছে যে মাথাটা তার একেবারেই নীচু হয়ে যাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।
মোট কথা পনের বছর বয়েস পর্যন্ত বহু আদর আর প্রশ্রয়ের মধ্যে চরিত্রের যে ভিত গড়ে উঠেছে রাখি গাঙ্গুলির, বিশ বছর বয়সের প্রতিকূল ধারার মধ্যে পড়ে সেটা বিপর্যস্ত হয়েছে শুধু–একটুও বদলায়নি।
এক বছর বাদে স্কুলেই চাকরি পেল। সরকারী স্কুলের চাকরি। অনেক ডিস্ট্রিক্ট স্কুলেই টিচার নেওয়া হচ্ছিল, এবারে তার ডিস্টিংশনের ছাপটাই কাজে লেগে গেল। এম. এ. বা অনার্স হলে আরো ভালো হত, মাইনে আরো কিছু বেশি পেত। যাই হোক, চেষ্টা-চরিত্র করলে কাছাকাছি থেকেই চাকরিটা করতে পারত। কিন্তু মনের আনন্দে সে দার্জিলিংয়ে চাকরি নিয়ে বসল। দার্জিলিং-এ থেকে চাকরি করবে এতে যেন নিজের কাছেই তার মর্যদা খানিকটা বেড়ে গেল। মনের আনন্দেই চাকরি করতে এলো।
কিন্তু এ আনন্দ খুব বেশিদিন থাকল না। গোড়ায় গোড়ায় হাতে যা পেত, ভাবত অনেক টাকা। কিন্তু কয়েকটা মাস না যেতে মাইনের অঙ্কটা কেমন জ্যোতিশূন্য ঠেকতে লাগল চোখে। তার প্রধান কারণ, সে হিসেব করে খরচ করতে জানে না। চোখে বা মনে কিছু ধরলে সেটার অধিকার না মেলা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। দার্জিলিংয়ের মতো জায়গায় শীতের ভব্যসব্য বেশবাসের ব্যবস্থাতেই অনেক খরচ। এ ব্যাপারে স্কুল। মিসট্রেস বলে সে মান খাটো করতে রাজি নয়। তার ওপর খাওয়া-দাওয়া আর প্রসাধনসামগ্রীর খরচ। মাস কাবার হবার আগে প্রতিবারই দস্তুরমতো ফাঁপরে পড়ে যায় রাখি গাঙ্গুলি।
এই কারণেই স্কুলের চাকরির ওপর বিরূপ সে। মাইনেটা আরো শদেড়েক টাকা বেশি হলেও মনের আনন্দে কাটাতে পারত। টিচাররা আর মেয়েরাও সৌখিনভাবে থাকে। আড়ালে তাকে নিয়ে কথাও হয়, এটুকু বাড়তি মর্যদার মতো। এর থেকে নেমে আসতে মন সরে না। সেই ছেলেবেলা থেকেই দৃষ্টি উঁচুর দিকে, তার কী দোষ! দোষ ভাবে না, কিন্তু মাসের শেষে মেজাজ ঠাণ্ডা রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।
.
এই শৈলশিখরেই সুবীরকান্তর সঙ্গে আলাপ এবং পরিণয় বিধিলিপি।
সুবীরকান্ত চক্রবর্তী:এখানকার কলেজের নতুন মাস্টার। নতুন বলতে দার্জিলিং এ নতুন। হুগলি না কোথাকার কোন কলেজ থেকে বদলি হয়ে এসেছে।
এ-সব পরের বৃত্তান্ত।
বিকেলে ম্যাল বা বাজারের দিকে সেজেগুজে বেড়াতে বেরিয়ে রাখি গাঙ্গুলির দিনকয়েক মনে হল দুর থেকে এক অল্পবয়সী ভদ্রলোক তাকে নীরবে লক্ষ্য করে। তা লক্ষ্য অমন অনেক সময় অনেকেই করে। এখানে মৌসুমের সময় বেড়াতে যারা আসে, পাহাড় দেখার সঙ্গে সঙ্গে তাদের যেন মেয়ে দেখে বেড়ানোর বাই চাপে। এ তো তবু তার দিকে চেয়ে থাকে, রাখি এও দেখেছে, নীচের থেকে বেড়াতে এসে এখানে খেটে আর মেহনতী করে খায় যে মেয়েগুলো, হ্যাংলার মতো লোকগুলো ওদের দিকে তাকিয়ে থাকে।…কিন্তু এ লোকটার তাকানোটা সে-রকম মনে হয়নি রাখির। বেশ পরিষ্কার চাউনি, আর বেশ একটু উৎসুক ভাব।
একদিন লেবংয়ের পথে দেখা হল। রাখি নামছিল আর লোকটা উঠছিল। ওকে দেখে দাঁড়িয়ে গেছল। রাখিও থামলে এগিয়ে এসে কথাই বলত হয়ত, কিন্তু রাখি দাঁড়ায়নি বা থামেনি। স্কুল-টিচারের এ-ধরণের গায়ে-পড়া আলাপ বরদাস্ত করা ঠিক নয়, এটুকু জ্ঞান তার আছে।
আর একদিন জলাপাহাড়ে দেখা। এই দিন আর আলাপ ঠেকানো গেল না। মাঝে মাঝে এসে বসে এখানে। সহকর্মিণীরাও সঙ্গে থাকে প্রায়ই। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ আসেনি, রাখি একাই বসে গুনগুন করে গান গাইছিল। এক সময়ে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে অদূরে লোকটা দাঁড়িয়ে। উৎসুক দৃষ্টি, ঠোঁটের ডগায় সামান্য। হাসির আভাস। চোখাচোখি হতে দুহাত জুড়ে নমস্কার জানিয়ে লোকটা এগিয়ে এলো।
–কিছু মনে করবেন না, আপনার নাম রাখি গাঙ্গুলি?
সরাসরি একেবারে নামের ওপর চড়াও না হলে এই আলাপের ইচ্ছেটা রাখি বাতিলই করে দিত। কারণ এক্ষুনি সুলতাদি বা মুখরা রমলাদি ওদের কেউ এসে গেলে জেরার চোটে রাখিকে অস্থির করে মারবে। কিন্তু অচেনা লোকের মুখে নিজের নাম শুনে বিরক্তির বদলে অবাক হল। মাথা নাড়তে আবার প্রশ্ন হল, আপনি। জলপাইগুড়ির মেয়ে আর ওমুকের ভাইঝি তো?
ছোট কাকার নামই করল। কিন্তু এবারের প্রশ্নটা কেন যেন খুব মার্জিত ঠেকল রাখির কানে।
এবারেও মাথা নেড়ে মৃদু প্রশ্ন করল, আপনি?
লোকটা জবাব দেবার আগে আরো একটু কাছে এগিয়ে এলো। পাশে বসেই পড়ে কিনা সেই ভয় রাখির। হাসিমুখে জবাব দিল, আমি জলপাইগুড়িতে আমার কাকার বাড়িতে অনেকবার কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছি। আমার কাকা আপনার কাকার খুব বন্ধু। তখন আপনাকে তিস্তার ধারে অনেকবার দেখেছি।
কাকার যে নাম করল, সেটা বিলক্ষণ চেনাই বটে। রাখির ছোট কাকার অন্তরঙ্গ বন্ধু শুধু নয়, সে বাড়িতে রাখি বা রাখির মায়ের যাতায়াতও আছে। ওদের বাড়ির মেয়েরাও তাদের বাড়িতে আসে। কিন্তু কাকার বন্ধুর ভাইপোর সঙ্গে আর আলাপ বাড়ানোর ইচ্ছে খুব নেই রাখির। সুলতাদি-রমলাদিরা আসার আগে সরে গেলেই ভালো হয়। তাই নিস্পৃহ একটা উক্তি বেরুলো গলা দিয়েও…।
কিন্তু লোকটার কেটে পড়ার ইচ্ছে নেই বোঝা গেল। হাসিমুখে বলল, আমার নাম সুবীরকান্ত চক্রবর্তী-এবার এখানে আসার আগেও জলপাইগুড়িতে কাকার বাড়ি হয়ে এসেছি। কাকা আপনার কথা বলছিলেন, আপনি এখানকার স্কুলে কাজ করছেন। …দেখা করে আলাপ করতে বলেছিলেন, আপনার কাকাও বলেছিলেন। হাসল। কিন্তু কদিন আপনাকে দেখেও ঠিক ভরসা পেয়ে উঠিনি। আর আপনার সঙ্গে প্রায়ই অন্য মেয়েরাও থাকেন…তাই একদিন আপনাদের বোর্ডিংয়েই যাব ভাবছিলাম।
আলাপে এগোতে ভরসা পেয়ে ওঠেনি পর্যন্তই শুনতে খারাপ লাগেনি। নিতান্ত সৌজন্যের খাতিরেই রাখি গাঙ্গুলি জিজ্ঞাসা করল, এখানে বেড়াতে এসেছেন?
এই সামান্য প্রশ্নটাই যেন একটা পাথর ছেড়ে পরের পাথরটায় বসে পড়ার পাসপোর্ট। কিন্তু জবাব যা পেল তা শোনার জন্যে খুব প্রস্তুত ছিল না রাখি গাঙ্গুলি। বলল, বেড়াতে এলে তো কবেই পালিয়ে বাঁচতাম। এসেছি এখানকার কলেজে মাস্টারি। করতে। কী কুক্ষণেই যে বদলি হতে রাজি হলাম!
কলেজের মাস্টার শুনে রাখি এবার এবং এই প্রথম কাছে থেকে ভালো করে দেখল মানুষটাকে। ছোট করে ছাঁটা চুল, চাকচিক্যশূন্য সাদামাটা মুখ–কেবল চাউনি ভারি পরিষ্কার আর উজ্জ্বল। চোখ দুটো লক্ষ্য না করলে মানুষটাকে নিরীহ বোকা। গোছের মনে হবে।
–এখানকার গভর্নমেন্ট কলেজে?
–হ্যাঁ, তাছাড়া আর বদলি হয়ে আসব কী করে? …এসে এই দুমাসের মধ্যেই। হাঁপ ধরে গেছে, এখন থেকেই কবে পালাতে পারব ভাবছি।
কলেজের মাস্টার শোনার পর আগের মতো আর অবজ্ঞার চোখে দেখা গেল না লোকটাকে। রাখি জিজ্ঞাসা করল, কেন?
-প্রথম কারণ, এখানকার অভদ্র রকমের শীত। একেবার জ্বালিয়ে মারলে। দ্বিতীয় কারণ, রাস্তাঘাট। হয় নাক উঁচিয়ে উঠতে হবে, নয়তো চোখ পায়ে ঠেকিয়ে নামতে হবে–আর তৃতীয় কারণটাই আসল, এখানে এ মাইনেয় পোযায় না, এখানে চাকরি করতে হলে মাইনে ডবল হওয়া উচিত।
জবাবটা বেশ স্বচ্ছ ঠেকল কানে। অথচ এই বয়সের লোকের শীতে কাবু হওয়া বা উঁচু-নীচু পথের দরুণ বিতৃষ্ণ হওয়া তেমন বীরোচিত সমস্যা বলে ঘোষণা করা উচিত নয়। আর শেষের উক্তির সঙ্গে রাখিও একমত। কিন্তু এই সামান্য আলাপের মধ্যে খরচায় না পোষানোর কথাটা রাখি গাঙ্গুলি অন্তত বলে ফেলতে পারত না। কিন্তু একজন কলেজের মাস্টার আর একজন স্কুল মাস্টারকে এ-কথা বলছে বলেই হয়ত ঝরঝরে স্পষ্টোক্তির মতো লাগল কথাগুলো।
পিছনে রমলাদির গলা শুনে রাখি সচকিত হয়ে ঘাড় ফেরাল। সুলতাদি আর রমলাদি দুজনেই এদিকে আসছে। রমলাদি বোধহয় পাথরে হোঁচট-টোচট খেয়েছে, তার গলা দিয়ে অস্ফুট একটা কাতর শব্দই বেরিয়ে এসেছে। সুবীরকান্তও ফিরে তাকিয়েছে। সুলতাদি হাসি চাপতে চেষ্টা করছে।
কাছে এসে দুজনেই গম্ভীর। রমলাদি আরো বেশি। সুবীরকান্ত তাদের উদ্দেশ্যে দুহাত কপালে তুলল। জবাবে তারা একবার মাথা নেড়ে সপ্রশ্ন গম্ভীর দৃষ্টিতে রাখির। দিকে তাকালো।
রাখি তাড়াতাড়ি পরিচয় করিয়ে দিল, ইনি এখানকার গভর্নমেন্ট কলেজের প্রোফেসার, সুবীরকান্ত চক্রবর্তী, দার্জিলিংএ নতুন এসেছেন–
সুবীরকান্ত সবিনয়ে বলল, প্রোফেসার হবার আশা শিগগীরই আছে বটে, তবে এখনো লেকচারার।
রমলাদি গম্ভীরমুখে সুলতাদিকে বলল, বোসো সুলতা। নিজেও একটা ছোট পাথরে বসে সদ্যপরিচিতের দিকে তাকালো।–আমরা স্কুলমাস্টার, তাই কলেজের ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকটরকেও প্রোফেসার বলে সম্মান দেখাই, আপনি হবু প্রোফেসার যখন, আমাদের চোখে প্রায় ভাইস প্রিন্সিপাল।
মাত্রা-ছাড়ানো রসিকতার কথা শুনে সুবীরকান্ত হাসতে চেষ্টা করল একটু। সুলতাদি ফস করে জিজ্ঞাসা করে বসল, রাখির সঙ্গে আগে আলাপ ছিল না, এখানে নতুন এসে আলাপ হল?
এদের এই বেশি-বেশি কথা বিচ্ছিরি লাগছিল রাখির। সুবীরকান্ত জবাব দিল, আলাপ আজই…তবে জলপাইগুড়িতে আগেও দেখেছি ওঁকে, আমার কাকা আর ওঁর কাকা বিশেষ বন্ধু।
–ও। রমলাদি গম্ভীরমুখেই মাথা নাড়ল।–সেই জন্যেই, নইলে কলেজের মাস্টাররা স্কুলের মাস্টারদের দিকে ফিরেও তাকায় না।
সুবীরকান্ত জবাব দিল, তা কেন, অবস্থা তো দুজনেরই সমান।
সুলতাদি যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল, ফোড়ন কাটল, দার্জিলিংয়ের উঁচু জায়গায় এসে আপনার দৃষ্টির আধোগতি হয়েছে দেখছি-কলেজে কী পড়ান, ফিলসফি নিশ্চয়ই?
-আজ্ঞে না, ইতিহাস।
ছদ্ম-বিস্ময়ে সুলতাদি তার সহচরীর দিকে ফিরল।-তুমিও তো ইতিহাস পড়াও রমলাদি, এ-রকম সাম্যবাদের কথা আছে নাকি কোথাও?
ঠোঁট উল্টে রমলাদি জবাব দিল, ঢের। সুলতান মামুদ নাদির, তৈমুর লং মন্দির দেখলেই ধ্বংস করেছে, ছোট বড় তফাত করেনি, আর খুন করার সময়ও মেয়ে-পুরুষে তফাত রাখেনি। তারপর ইংরেজ… হিন্দু মুসলমান ফরাসী শিখ–কাউকে ছোট করে দেখেনি, সক্কলের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে।
দুই মহিলার দ্বারা এ-ভাবে আক্রান্ত হয়ে আঁর শেষে সাম্যবাদের এই বেপেরোয়া বিশ্লেষণ শুনে সুবীরকান্ত গোবেচারার মতো হাসতে লাগল। রাখি ভাবছে, লোকটা বুদ্ধিমান হলে এবার তার উঠে পালানো উচিত।
সুলতাদি বলল, রমলাদি একটু বেশি কথা বলেন, আপনি কিছু মনে করবেন না যেন।
হাসিমুখে মাথা নেড়ে সুবীরকান্ত এবারে উঠেই দাঁড়াল।–না, এখানে এসে পর্যন্ত একঘেয়ে লাগছিল, আলাপ হয়ে আজ সময়টা বরং ভালই কাটল। আচ্ছা, আবার দেখা হবে নিশ্চয়
সুলতাদি সায় দিল, নিশ্চয়, আমরা তো প্রায়ই আসি এখানে।
সকলের উদ্দেশে নমস্কার জানিয়ে সুবীরকান্ত প্রস্থান করল। সেদিকে খানিক চেয়ে থেকে রমলাদি ডাকল, রাখি–
এবারে তাকে নিয়ে পড়বে ওরা, রাখি ভালই জানে। সদ্যপরিচিত একটা লোকের সামনে এই গোছের বাঁচালতা তার ভালো লাগছিল না। ডাক শুনে তাকালো শুধু।
-একটা গান কর তো!
রাখি কোনদিন গান করেও নি, গান জানেও না। কিন্তু এই ফর্মাসের তাৎপর্য বুঝেছে। এই দুজনের মধ্যে রমলাদির মুখখানাকেই সকলে বেশি সমঝে চলে। বয়েস ছত্তিরিশ, দেখতে ভালো নয়, বিয়ে-থা হবার আশা নিজেও আর রাখে না। কিন্তু এতটুকু রসের হদিস পেলে আর রক্ষা নেই।
–তোমার প্রাণে বাতাস লেগে থাকে তো তুমি করো!
টেনে টেনে রমলাদি বলল, লেগেছে, ছত্তিরিশের প্রাণে বাহাতুরে বাতাস, গান। কর না একটা, আজ বোধহয় চেষ্টা করলে পারবি!
রাখি হেসে ফেলল।
অমনি সোজা হয়ে বসে চোখ পাকালো রমলাদি।–আবার হাসি! বলি, এক কাকার ভাইপোর সঙ্গে আর-এক কাকার ভাইঝির কিছু একটা হয়ে-টয়ে যাবার সম্ভবনা আছে?
রাখি প্রায় রাগ করেই বলল, তুমি একটি অসভ্য!
–ও! আর নিজেরা যে নিরিবিলিতে ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসেছিলি? স্কুলের কোনো মেয়ে দেখে ফেললে?
রাখি প্রতিবাদ করল, ঘেঁষাঘেঁষি, মানে! ভদ্রলোক তো ওই পাথরে বসেছিল।
সুলতাদি ইন্ধন যোগালো, পাহাড় কিনা, নীচে থেকে ঘেঁষাঘেঁষি মনে হয়।
–হোক। পাহাড়টা কী আমার, ভদ্রলোক এসে বসলে কী করব?
রমলাদি তক্ষুনি জবাব দিল, দুটো কাজ করতে পারতিস। আসামাত্র বলে উঠতে পারতিস, এসো নাথ, আমি উমা, শিবের তপস্যায় এই শৈলশিখরে বসে মাথা খুঁড়ছি! নয়তো এসে বসামাত্র পাথর তুলে তাড়া করতে পারতিস! কিছুই যখন করলি না, বুঝতে হবে তোর মনে অনিশ্চয়তার পাপ ঢুকেছে।
নিরুপায় রাখি আবারও হেসেই ফেলল।
এখানেই যে প্রজাপতির নির্বন্ধ সেটা রাখি দিনকতকের মধ্যেই জেনেছে। আর সেটা এমন আচমকা জানা যে সে হকচকিয়ে গেছল।
তার আগে কটা দিন সুবীরকান্তর সঙ্গে প্রায় রোজই দেখা হয়েছে। কোনদিন রমলাদি-সুলতাদির সামনে, কোনোদিন বা একা। এই দেখা হয়ে যাওয়াটা যে লোকটার সক্রিয় চেষ্টার ফল সেটা বুঝতে বেগ পেতে হয়নি। রমলাদি-সুলতাদির ঠাট্টা-তামাসায় নাজেহাল হয়ে লোকটার প্রতি রাখি বলতে গেলে একটু বিরক্তই তখন।…কলেজের মাস্টার, এমনিতে হাবভাব গম্ভীর, কিন্তু তার মধ্যেই তার প্রতি উৎসুক-উৎসুক ভাবটা রাখি টের পায়। রমলাদি সুলতাদি আরো বেশি টের পায়। তাকে একলা দেখলে যেন আরো বেশি খুশি হয়। গায়ে পড়ে নিজের কাকার কথা বলে, ওর কাকার কথা, বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করে, স্কুলে কী পড়ায়, উঁচু ক্লাসে পড়ায় কিনা খোঁজ নেয়–আর কিছু কথা না পেলে রমলাদি-সুলতাদির প্রশংসা করে।
রাখিও মনে মনে বলে–সুবীরকান্ত না হ্যাংলাকান্ত!
কিন্তু আচমকা সেদিন এক অভাবিত মানসিক বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেল রাখি গাঙ্গুলি।…রমলাদি আর সুলতাদির সঙ্গেই জলাপাহাড়ের দিকে যাচ্ছিল, কিছুদূরে ওই মূর্তি। গম্ভীর মুখে যেন তারই প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। রমলাদি গলা দিয়ে একটা চাপা শব্দ বার করে রাখিকে বলল, একটু ভাওতাবাজী করব?
–যা খুশি করগে। ভ্রুকুটি করে রাখি জবাব দিল।
–আচ্ছা তুই বোসগে যা। বলেই সুলতাদির হাত ধরে টেনে রমলাদি ভাঁওতাবাজী করতে চলল। রাখি একাই তাদের বসার জায়গায় উঠে গেল।
কিন্তু মিনিট সাতেক না যেতেই অবাক সে। তক্ষুনি বুঝে নিল রমলাদি ভাওতাবাজীটা আসলে কার সঙ্গে করেছে। তার দিকেই একলা উঠে আসছে সুবীরকান্ত, ওরা দুজন নিপাত্তা।
কাছে এসে সামনের পাথরটায় বসে পড়ল। তাড়াতাড়ি ওঠার দরুণ অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে। বলল, এ-রকম শরীর খারাপ নিয়েও পাহাড়ে ওঠা-নামা করেন কী করে, আশ্চর্য! তার ওপর আজ সমস্ত দিন কিছু খাননি শুনলাম!
রাখির রাগই হচ্ছে, সেই সঙ্গে বিব্রতও কম নয়। জবাব না দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ওঁরা কোথায়?
–ওঁরা বাজারের দিকে গেলেন। বললেন, শরীর খারাপ তাই আপনার জন্যে ফল কিনতে যাচ্ছেন, আর আমাকে বললেন, গল্প করার ইচ্ছে থাকলে ওপরে চলে। যান। হাসল। রমলা দেবী আবার ঠাট্টা করলেন, আমার বরাতেও কিছু ফল-টল জুটতে পারে।…আমি বেশ পেটুক আছি জানেন, এবারে আসার আগে আপনার মা আমাকে একদিন খুব যত্ন করে খাইয়েছিলেন…কী চমৎকার রান্না তার!
কী থেকে কী কথা! রাখি অবাক, আমার মা?
-হ্যাঁ, কাকা নিয়ে গেছলেন। খুব ভালো লেগেছিল তাকে।
রাখি ভেবেই পেল না তার মা হঠাৎ এই লোককে আদর-যত্ন করে খাওয়াতে গেল কেন? সুবীরকান্ত অন্তরঙ্গ সুরে জিজ্ঞাসা করল, যাক, আপনার কী হয়েছে বলুন তো?
-কিছু না।
সমস্ত দিন কিছু খান নি শুনলাম যে?
–খেয়েছি। ঈষৎ বসুরে জবাব দিল, তাছাড়া দার্জিলিংয়ের বাতাস খেলেও কিছু কাজ দেয়।
-বলেন কি! আমার তো উল্টে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খিদে পায়! হাসছে।…ওঁরা তাহলে ঠাট্টা করেছেন, আমি কিন্তু আজ সত্যি আপনাকে খুঁজছিলাম–দেখা না হলে হয়ত আপনার বোর্ডিংয়েই চলে যেতাম।
রমলাদি আর সুলতাদির জন্যেই মেজাজ প্রসন্ন নয় রাখির। অন্তরঙ্গ উক্তিটা তাই স্পর্ধার মতো ঠেকল কানে। জিজ্ঞাসু দুচোখ তার মুখের ওপর থমকালো।
সুবীরকান্ত বলল, সামনে চার দিন ছুটি আছে, আপনাদেরও ছুটি নিশ্চয়, ভাবছি একবার জলপাইগুড়ি ঘুরে এলে হয়।…যাবেন?
–না।
এ-রকম সাদাসাপ্টা জবাব আশা করেনি সুবীরকান্ত। মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে আবার বলল, ছুটির মধ্যে এখানে বসে থেকে কী করবেন, চলুন না একসঙ্গে ঘুরে আসি।
রাখির রাগ চড়ছে। মাসের শেষে হাত খালি, ইচ্ছে থাকলেও যাওয়া হত না। কিন্তু অসহিষ্ণুতার আসল কারণ, লোকটার হ্যাংলামি দেখে। মাত্র কটা দিনের আলাপে এ-রকম অনুরোধ করার মতো অন্তরঙ্গতা কিছু হয়নি। কিন্তু কলেজের মাস্টারের সঙ্গে কত আর অভদ্র ব্যবহার করতে পারে। আবারও সংযত জবাবই দিল, না, আমার যাওয়া সম্ভব নয়।
একটু চুপ করে থেকে লোকটা দ্বিধান্বিত মুখে হাসল একটু। তারপর বলল, আপনি বোধহয় বিরক্ত হচ্ছেন, কিন্তু এদিকে আমি একটু মুশকিলে পড়ে গেছি…যাবেন না যখন, বোঝাপড়াটা এখানেই সেরে নিই…আপনার সত্যই শরীর খারাপ নয় তো?
এবারে রাখি অবাক। গোড়া থেকেই আজ কথাবার্তার সুর অন্যরকম ঠেকছিল কানে। জবাব না দিয়ে মুখের দিকে তাকালো শুধু।
সুবীরকান্ত পকেট থেকে খাম বার করল একটা। তারপর সেটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, দার্জিলিংয়ে আসার পর আমার কাকার এই তিন নম্বর চিঠি। পড়ুন
বিস্ময়ের ওপর বিড়ম্বনা।–আমি কেন!
-আপনার আর আপনার মায়ের ব্যাপার নিয়ে লেখা। পড়ুন।
–রাখি খামটা নিল। খুলল। কিন্তু পড়তে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে দেহের রক্তকণাগুলো বুঝি মুখের দিকে ছোটাছুটি আরম্ভ করে দিল। একটু অনুযোগের সুরেই ভাইপোকে কাকা লিখেছেন, এর আগে দুদুটো চিঠি লিখেও আসল প্রসঙ্গের জবাব পাননি। দার্জিলিংয়ে আসার সময় সে কথা দিয়ে গেছল রাখি গাঙ্গুলির সঙ্গে দেখা করে এবং আলাপ করে তার মতামত জানাবে। এদিকে ভদ্রমহিলা (রাখির মা) আশায় দিন গুনছেন আর প্রায় রোজই খোঁজ নিচ্ছেন ভাইপোর মতামত কিছু জানা গেল কিনা। ভরসা পেলেই মেয়েকে তিনি চিঠি লিখতেন। কোনো খবর না পেয়ে মহিলা ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছেন। কাকা লিখেছেন, পছন্দ যদি না-ই হয়ে থাকে তো এভাবে ঝুলিয়ে না রেখে সেটা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে অসুবিধে কি? শেষের মন্তব্য, তাঁর মতে মেয়েটি ভালো এবং অপছন্দের নয়, ভাইপো এখানে বিয়ে করলে ব্যক্তিগতভাবে তিনি খুশিই হতেন।
চিঠি শেষ করতে গিয়ে দার্জিলিংয়ের পাহাড়ে বসেও রাখি ঘেমে ওঠার দাখিল। চিঠি খামের মধ্যে পুরে রাখতে গিয়েও হাত কাঁপছে যেন। ও যতক্ষণ চিঠি পড়ছিল, সুবীরকান্ত ওর মুখের ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারেনি। বিড়ম্বিত রমণী-মুখের এমন মিষ্টি কারুকার্য আর বুঝি দেখেনি! হাত বাড়িয়ে খামটা নিল।
রাখি আর এদিকে ফিরে তাকাতেও পারছে না।
একটু অপেক্ষা করে সুবীরকান্ত বলল, এখন আমার মত আমি জানাতে পারি, কিন্তু একতরফা মতের উপর তো কিছু নির্ভর করছে না, কী জবাব দেব বলুন?
নিজেকে রাখি বচনপটু বলে জানত। কিন্তু এখন আর গলা দিয়ে শব্দ বেরুতে চায় না। এমন আচমকা বিড়ম্বনার মধ্যে জীবনে পড়েনি। সামনের দিকে চোখ রেখেই বলল, এ সম্পর্কে আমি কিছু ভাবিনি।
–ঠিক কথা।…আপনার মা আপনাকেও লিখলে পারতেন, তাহলে এ-রকম বিব্রত বোধ করতেন না। তার বোধহয় ধারণা, আমার মত পেলেই আটকাবে না। সে যাক, আপনার ভাবার সুবিধের জন্যে নিজের সম্পর্কে দুই-একটা কথা বলে রাখি। জলপাইগুড়ির ওই এক কাকা ছাড়া আমার তিনকুলে আর কেউ নেই। ম্যাট্রিক থেকে এম.এ. পর্যন্ত স্কলারশিপের টাকায় পড়েছি। বি.এ. আর এম. এ. দুটোতেই ফার্স্টক্লাস পেয়েছি। একেবারে প্রোফেসারি পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পিছনে সুপারিশের জোর না থাকায় লেকচারারের পোস্ট অ্যাকসেপ্ট করতে হয়েছে, আর এক-আধ বছরের মধ্যে প্রোফেসার হব আশা করাটা খুব বেশি হবে না বোধহয়।
এতগুলো কথা শোনার ফাঁকে রাখি কখন এদিকে মুখ ফিরিয়েছিল জানে না। কথা শেষ হতে খেয়াল হল দুজনে দুজনার দিকে চেয়ে আছে। তাড়াতাড়ি মুখ ফেরাল আবার।
সুবীরকান্ত উঠে দাঁড়াল।–আচ্ছা আর বিরক্ত করব না, ভেবে আমাকে জানাবেন।
চলে যাচ্ছে। রাখি সেদিকে চেয়ে আছে। যতক্ষণ দেখা গেল চেয়েই রইল। তারপর খেয়াল হল, রমলাদি সুলতাদি এক্ষুনি ফিরে এসে তাকে নিয়ে পড়বে।
উঠে হনহন করে সেও বোর্ডিংয়ের উদ্দেশে নেমে চলল। গিয়ে কোন রকমে ঘরের দরজা বন্ধ করতে পারলে হয়। ভিতরটা কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছে। তার। আবার সেই সঙ্গে মনে হচ্ছে, পাহাড়ী শহরটার রঙ যেন এক মুহূর্তে বদলে গেছে।…প্রথম দিন এসে আলাপ করা থেকে এ-পর্যন্ত লোকটার কোনো আচরণই এখন আর বিসদৃশ লাগছে না।
.
কটা দিনের মধ্যে রাখি আর বোর্ডিং ছেড়ে বেরুতেই পারল না। কী একটা সঙ্কোচ যেন পায়ে জড়িয়ে আছে তার।
নিজের বিয়ের সম্পর্কে ওর নিজেরই কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। বিয়ের কল্পনা করেনি এমন নয়–করেছে যখন বেশ ঘটা করেই করেছে। কল্পনায় ঘটা করতে দোষ। কী? সেই সম্ভাব্য জীবনের মানুষকে একসময় সর্ব-যোগ্যতার চূড়ায় তুলেও বসিয়েছে। তার সঙ্গে আর যাই হোক, কলেজের মাস্টার সুবীরকান্ত চক্রবর্তীর মিল। নেই। কিন্তু নিজের এই সংগোপন কল্পনাটাকে রাখি গাঙ্গুলি বাস্তবের মর্যাদা কখনো দেয়নি। বরং আচমকা যে মানুষটা এগিয়ে এসেছে তাকেই এখন অন্যরকম লাগছে।…চেহারা সাদামাটা হলেও চোখদুটো ভারী উজ্জ্বল। কথাবার্তাগুলোও স্পষ্ট আর স্বচ্ছ। ম্যাট্রিক থেকে এম.এ. পর্যন্ত স্কলার, এও খুব কম কথা নয়। তার ওপর স্কুল-মাস্টার তো নয়, প্রোফেসার। প্রোফেসার আর লেকচারারে এখনো খুব তফাত দেখে না সে।
….সেদিনের নিজের ব্যবহারে রাখি নিজেই লজ্জা পাচ্ছে। কী করে জানাবে ভিতরে ভিতরে এই ব্যাপার চলেছে। রমলাদি আর সুলতাদির ঠাট্টাতামাসা–কলেজ-মাস্টারের হ্যাংলামি ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেনি। চারদিনের ছুটি শুয়ে বসে কেটে যাচ্ছে, একসঙ্গে জলপাইগুড়ি গেলেও মন্দ হত না। অন্তত ওরকম ঠাসঠাস জবাব না দিলেও
আবার বিয়েটা এখানে যে হয়েই যাবে, চিন্তার এই নিশ্চিত প্রশ্রয়েও গা ভাসাতে পারছে না।…বিয়ের বাজারে এই সব ছেলের দামও কম নয়। কতটা আশা করে বসে আছে, ঠিক কি? যদিও খুব বেশি আশা করছে বলে তার মনে হয় না। তবু তাকে এখানে এই বড়লোকী চালে থাকতে দেখে কী ভেবে বসে আছে ঠিক কী? তাদের বাড়ি-ঘরের ভেতরের অবস্থা ঠিকঠিক জানে কী না তাই বা কে জানে!..মায়ের তো ওই পাঁচ হাজার টাকা সম্বল!
চিন্তা যে ভাবেই করুক, বাইরে বেরুবার জন্যে ভেতরটা কদিন ধরে ছটফট করছিলই। সেদিন সকালে মায়ের একটা চিঠি পেল। অন্যান্য পাঁচকথার পর মা লিখেছে, ওমুকের ভাইপো সুবীরকান্ত নামে একটি ছেলের সঙ্গে তার ইতিমধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে কিনা জানাতে। ছেলেটি এখানকার কলেজের প্রোফেসার। তাকে দেখে আর তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে খুবই ভালো লেগেছিল। আশা ছিল, নির্বন্ধ থাকলে এখানেই রাখির বিয়েটা দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারবে। তার কাকাও আশা দিয়েছিল। এতদিনেও কোনো খবর না পেয়ে মনে হচ্ছে–হবে না। ছেলেটির হয়ত আরও বড় ঘরে বিয়ে করার ইচ্ছে। তবু এ-রকম কোনো ছেলের সঙ্গে কখনো দেখা হয়েছে কিনা মেয়েকে জানাতে লিখেছেন।
সেই বিকেলেই রাখি চুপচাপ একা না বেরিয়ে পারল না। রাস্তায় নেমেই বুকের ভেতরটা কেমন ঢিপঢিপ করতে লাগল।
জলাপাহাড়েই উঠল।
কেউ কোথাও নেই।…নিজে থেকে এসে আন্দাজে কোথায় খুঁজবে? একবার ভাবল ম্যালের দিকটা ঘুরে এদিকে এলে পারত। আবার ভাবছে সেটা যেন বেশি বেশি হবে। পরিচিত জায়গাটা ছেড়ে আরো খানিকটা পিছনদিকে পাহাড়ের আড়ালে গিয়ে বসল। এরও মনস্তত্ত্বগত কারণ আছে। রমলাদি সুলতাদি এসে পড়লে দূর থেকে দেখে ভাববে কেউ নেই। কিন্তু যে কারণে এই সাবধানতা, তারই দেখা মিলবে কিনা কে জানে!
বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। দেখা মিলল। কাছে এসে দাঁড়াল। আগের দিনের মতো সামনে বসে পড়ল না। বলল, সেদিন ও-কথা বলে আপনাকে এতটা বিব্রত বা বিরক্ত করা হবে বুঝতে পারিনি। কটা দিন আপনার বেরুনোই বন্ধ হয়ে গেল! যাক, আপনার দিক থেকে কোনো সঙ্কোচের কারণ নেই, ও ব্যাপারে স্বাধীন মতামত তো সকলেরই থাকা স্বাভাবিক। কিছু মনে করবেন না, দ্বিতীয়বার আর বিরক্ত করব না।
রাখি ফাঁপরে পড়ল। ও যে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে–এই রকমই ভাবা স্বাভাবিক। …এবারে চলেই যাবে বোধহয়। অতএব তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল, আপনি জলপাইগুড়ি যান নি?
সুবীরকান্ত হাসল একটু। প্রশ্নটা যেন আশাপ্রদ ঠেকল কানে। বলল, যে জন্যে যাবার চিন্তাটা মাথায় এসেছিল তার আলোচনা তো এখানেই হয়ে গেল। এরপর কিছু না জেনে সেখানে একলা ছুটে লাভ কী?
রাখি নীরব আবার। কী ভাবে যে প্রাসঙ্গিক আলাপটা শুরু করবে ভেবে পাচ্ছে না।
–আপনি কী ভেবেছিলেন আমি জলপাইগুড়ি চলে গেছি?
এবারে রাখি একটু বুদ্ধিমতীর মতো কাজ করল। হাঁ-না কিছুই জবাব না দিয়ে। অল্প একটু হেসে বলল, বসুন।
কদিনের মধ্যে দেখা না মেলার একটাই অর্থ ধরে নিয়েছিল সুবীরকান্ত। তাকে এড়াবার চেষ্টা। কিন্তু এই সামান্য অভ্যর্থনার ফলেই সংশয় দেখা দিল। সামনের পাথরে বসে ঈষৎ আগ্রহ নিয়েই তাকালো তার দিকে।
অন্য দিকে চোখ রেখে মৃদু গলায় রাখি বলল, আজ সকালে আমিও মায়ের চিঠি পেয়েছি।
আরো কিছু শোনার আশায় সুবীরকান্ত অপেক্ষা করল একটু। তারপর জিজ্ঞাসা। করল, আমি কী ধরে নেব, আমার সেদিনের প্রস্তাবটা বাতিল হয়ে যায় নি?
চোখ তুলে রাখি একবার তার দিকে না তাকিয়ে পারল না। আর তার পরেই সঙ্কোচ কেমন কমে আসতে লাগল। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, আমাদের বাড়ির সব খবর আপনার জানা আছে?
সুবীরকান্ত অবাক একটু।–কী খবর?
আরো মৃদু সুরে রাখি জবাব দিল, আমাদের বাড়ির অবস্থা-টবস্থা…
বলার পর নিজেরই বিচ্ছিরি লাগল রাখির। অনুরাগ-পর্বের যেটুকু জানা আছে। তাতে কোনো মেয়ে নিজে মুখ ফুটে এ-কথা বলেছে বলে শোনেনি। ওদিকে বক্তব্যটা বোধগম্য হতে সুবীরকান্ত তার দিকে চেয়ে হাসছে মিটি মিটি। বলল, কাকা কিছু কিছু বলেছেন, কিন্তু ও নিয়ে আমি মাথা ঘামানো দরকার মনে করিনি।…আমি গরিবের ছেলে, রাজত্ব বা রাজকন্যার আশা রাখি না, শুধু মনের মতো একটি কন্যা পেলেই খুশি।
কথাগুলো কান পেতে শোনার মতো। রাখির সমস্ত মুখে লালের আভা ছড়াচ্ছে। হাসছে অল্প অল্প। হাওয়া অনুকূল সেটা সুবীরকান্ত বুঝে নিয়েছে। তাই আরো কিছু বলার লোভ সংবরণ করতে পারল না। সামনের দিকে আর-একটু ঝুঁকল। হাসছে।–বললে বিশ্বাস হবে কিনা জানি না, বছর আটেক আগে একবার কাকার কাছে এসে তিস্তার চরে কতগুলো মেয়েকে হুটোপুটি করতে দেখতাম। তার মধ্যে একটি মেয়েকেই ভারী জীবন্ত মনে হত আমার। তারপর আরো অনেকবার এসেছি, অনেকবার দেখেছি, কিন্তু দার্জিলিংয়ে এসে কাকা যে সেই মেয়েকেই দেখতে বলে দিয়েছিলেন এতবার করে, কী করে জানব!
লজ্জা সত্ত্বেও রাখি আবার তার চোখ না তুলে পারল না। এই মুহূর্তে যেন একটা অদ্ভুত ভালো লাগার স্বাদ তার অস্তিত্ব ভরাট করে তুলছে।
সুবীরকান্ত সরাসরি কাজের কথায় চলে এলো এবার।–এখন তাহলে আমি আমার কাকাকে চিঠি লিখতে পারি?…হাঁ কী না বলো?
মুখে বলা গেল না। রাখি হাসিমুখে মাথা নেড়ে সায় দিল। পুরুষগুলো এত চট করে আপনি থেকে তুমিতে চলে আসে কী করে ভেবে পায় না!
ভাবতে না পারার আরও একটু বাকি ছিল। মাথার ওপর একটা চলতি মেঘ যে আরো একটু আচমকা কৌতুক বর্ষণের জন্যে এগিয়ে এসেছিল দুজনের কেউ লক্ষ্য করেনি। হঠাৎ একপশলা বৃষ্টিতে সচকিত দুজনেই। রাস্তায় বেরুলে এখানে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতোই ছাতা একটা থাকে সঙ্গে। সুবীরকান্তর সঙ্গে ছাতা আছে, কিন্তু বেরুবার তাড়ায় রাখি ছাতা আনতে ভুলে গেছে। চট করে নিজের ছাতাটা খুলে এগিয়ে এলো, তারপর রাখির গা ঘেঁষে ওই পাথরটাতেই বসে পড়ল।
দুজনে অনায়াসে বসার মত বড় নয় পাথরটা। রাখি আড়ষ্ট একটু। গায়ে গা ঠেকছে, কাঁধে কাধ লাগছে। তাছাড়া অন্তরঙ্গ না হলে পাঁচমিনিটের বৃষ্টির ঝাঁপটায় সর্বাঙ্গ ভিজবে। কিন্তু পাশের লোকের তাকে ভিজতে দেবার ইচ্ছে নেই। বৃষ্টির ধারা আরো জোরে নামতে একেবারে গায়ের সঙ্গে লেগেই বসল। ওদিকে আচমকা বৃষ্টির প্রথম ঝাঁপটাতেই রাখির মুখ আর মাথার খানিকটা ভিজে গেছে।
সুবীরকান্ত হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করল, আজ ছাতা আনোনি যে?
–ভুলে গেছি।
সুবীরকান্ত বলল, ভুলের জন্যে কৃতজ্ঞ।
রাখিও হেসেই ফেলল।
পাঁচমিনিটের বৃষ্টি। মেঘটা চলে যেতেই ঝলমলে আলো। যেন রসিকতা করার জন্যই আসা। ছাতা বন্ধ করে সুবীরকান্ত পকেট থেকে রুমাল বার করে হাতমুখ মুছতে গিয়ে দেখে রাখি তার ব্যাগ খুলে রুমাল খুঁজছে। ব্যাগে রুমাল নেই, অর্থাৎ তাও ভুলেছে।
হাসিমুখে সুবীরকান্ত নিজের রুমাল এগিয়ে দিল। দ্বিধা দেখে রুমালটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, বিপাকে পড়লে লজ্জা করতে নেই!
অগত্যা তার রুমালেই মুখ মুছল রাখি। শরীরে কী এক অজানা অনুভূতি শিরশির করছে। রুমালটা তার হাতে ফেরত দিয়ে হাসিমুখে বলেই ফেলল, এটা বিপাক! ২৬০
রুমালটা দিয়ে বেশ চেপে চেপে নিজের মুখ মুছল সুবীরকান্ত। একটা লোভনীয় স্পর্শ যেন ওতে লেগে আছে। জবাব দিল, দুজনের দুরকমের বিপাক। তোমার বিপাক জলটা এল বলে, আর আমার বিপাক ওটা এত চট করে থেমে গেল বলে।… এবারে বোধহয় ভদ্রলোকের মতো আমার ওই পাথরটাতে উঠে যাওয়া উচিত।
হাসছে রাখিও। চোখের কোণে দুষ্টুমি। অল্প মাথা নাড়ল। অর্থাৎ তাই উচিত।
সুবীরকান্ত তক্ষুনি আবার বলল, কলেজের মাস্টার তো, উচিত কাজ করে করে ওটার ওপর একেবারে অরুচি ধরে গেছে। যেতেই পারে–তুমি কী বলে?
মুখের দিকে চেয়ে রাখি এবারে বেশিই হেসে ফেলল। জবাব দিল, আমিও স্কুলের মাস্টার।
সুবীরকান্ত মহা উৎফুল্ল। ওইটুকু পাথরের মধ্যেই মুখোমুখি ঘুরে বসার চেষ্টা।–তার মানে তোমারও অরুচি ধরেছে? ওয়ারফুল!
রাখির ভালো লাগছে বটে, আবার ভাবগতিক দেখে ভয়ও করছে। রুচি বদলাবার আশায় আরো কী করে বসে ঠিক কী! কলেজের ছেলে বা স্কুলের মেয়ে এসে হাজির হতে পারে, আর সুলতাদি রমলাদি কেউ এ অবস্থায় দেখলে ওকে আস্ত রাখবে কিনা সন্দেহ।
সুবীরকান্ত হাসতে হাসতে বলল, আজ এই বরাত আমার কল্পনাও করিনি, ভেবেছিলাম তোমাকে সেদিন বিব্রত করার জন্যে দুটো পোশাকী কথা বলেই চলে যেতে হবে। পরের মুহূর্তে কী মনে পড়তে আঁতকে উঠল যেন।–কী সর্বনাশ!
কেউ এসেই গেছে ভেবে সচকিত হয়ে রাখি এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। কাউকে না দেখে বিমূঢ় দৃষ্টি গা-ঘেঁষা-লোকটার দিকে ফেরালো।
সুবীরকান্ত বলে উঠল, এটা তো শ্রাবণ মাস এসে গেল!
দুশ্চিন্তার কারণটা সঠিক বোধগম্য হল না। রাখি চেয়েই রইল।
–ভাদ্রয় বিয়ে নেই, আশ্বিনে বিয়ে নেই, কার্তিকে বিয়ে নেই! তোমাকে কাল পরশুর মধ্যেই ছুটি নিতে হচ্ছে, তারপর চলো দুজনে জলপাইগুড়ি পালিয়ে গিয়ে কাজটা সেরে আসি আমার অত দেরি সহ্য হবে না।
তার চোখে চোখ রেখে রাখি হাসতেই লাগল।
.
বিয়ে হয়ে গেল। সেটা এত সহজে হল যে রাখির ভাবতেই অবাক লাগে। এই বিস্ময়ের সঙ্গে একটা রোমাঞ্চকর বিহ্বলতার মধ্যে দুটো মাস কেটে গেল।
তারপর শ্রীমতী রাখি চক্রবর্তী ধীরেসুস্থে তার শ্রীচক্রবর্তাটিকে নতুন করে আবিষ্কার করতে লাগল। তার প্রথম চোখ গেল লোকটার পড়ার নেশার দিকে। বই পড়ে লোক এত আনন্দ কী করে পায়, রাখি ভেবে পায় না। ফি-মাসে পার্শেলে কলকাতা থেকে বই আসে। তার বই যে কলেজের পাঠ্যবই-এর অন্তর্গত তা নয়, আবার ওই সব পড়ার ব্যাপার নিয়ে আলোচনার উৎসাহও কম নয়। ফলে রাখির ধৈর্য ফুরোতে সময় লাগে না। কিন্তু মনোযোগ দিয়ে শোনার ভান করেই কাছে এগোয়। লেকচার শুনতে শুনতে এক সময় চুপি চুপি বইটা সরিয়ে ফেলে। তারপর আলস্যভরে বুকের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে হাই তুলে বলে, তারপর?
ফলে তারপর যা সেটা কোনো আলোচনার বিষয় নয়।
আবার কোনো সময় বা লেকচার শুনতে শুনতে টান মেরেই হাতের বই ফেলে দিয়ে নিজের দুই ঠোঁট দিয়ে খানিকক্ষণ পর্যন্ত ওই মুখ বন্ধ করে রাখে। শেষে নিরীহ মুখে জিজ্ঞেস করে, তারপর?
রাখি লক্ষ্য করেছে, এই একটি মাত্র উপায় ভিন্ন লোকটাকে পড়াশুনার জগৎ থেকে অন্য দিকে টেনে আনা খুব সহজ নয়।
তার দ্বিতীয় আবিষ্কার, লোকটা স্নেহ আর দরদের কাঙাল। খুব অল্পবয়সে বাপ মা হারিয়েছে, আর আপনার বলতে তেমন কেউ নেই বলেই বোধহয়। ওর কাকা বা রাখির মা চিঠিতে আদর করে দুকথা লিখলেই ভারী খুশি। দুজনের সংসারে কমবাই-হ্যাণ্ড গোছের একটা লোক রাখা হয়েছে। প্রেসার-কুকারে রান্না সে-ই করে নটা না বাজতে রাখি স্কুলে ছোটে, আসতে তো বিকেল। এরই মধ্যে ছুটির দিনে ও যদি মানুষটার জন্যে বাড়তি একটু খাবার-দাবার করে, তাতেই আনন্দে আটখানা। মাঝে একদিন সর্দিজ্বর হয়েছিল। স্কুল থেকে ফিরে রাখি সেদিন আর বেরোয়নি, শিয়রের কাছে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। সেটা যে বিশেষ কিছু করা, রাখির মনেও হয়নি। কিন্তু একটু বাদেই অবাক সে। দুচোখ যেন ছলছল করছে।
রাখি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল কষ্ট হচ্ছে খুব?
মুখের দিকে চেয়ে থেকেই আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছে, কষ্ট হচ্ছে না। বলেছে, কত সময় অসুখে পড়ে থাকতাম, ওঠার শক্তি নেই, হামা দিয়ে গিয়ে এক গেলাস জল গড়িয়ে খেতে হয়েছে।…আর আজ?
রাখিরও বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠেছিল, মনে আছে নিজের গালটা তার কপালের ওপর ছিল।
তৃতীয় ব্যাপার লক্ষ্য করেছে, মানুষটার গোঁ-ভরা অভিমান। প্রত্যাশা বেশি বলেই অভিমান বেশি। রাখি আগে স্কুলে চলে যায়। কিন্তু একটা দিন তার জামা-কাপড় ঠিক-ঠাক করে না রেখে গেলে ময়লা জামা-কাপড় পরেই কলেজে চলে যাবে। ভুল করে নয়, ইচ্ছে করে। তারপর ফিরে এসে অভিমান–অর্থাৎ বাক্যালাপ কম, চুপ।
রাখি হয়ত বলল, তোমার কি নিজের চোখ নেই? আমার মনে ছিল না বলে এই জামা-কাপড়ে কলেজ করে এলে?
জবাব, এলাম–এরপর যাতে তোমার মনে থাকে সেই জন্যে!
আর একদিনও এই ভুল হয়েছিল। সেদিনও একই ব্যাপার। মিষ্টিকথায় দুই-এক কথায় নিজের ভুলের কথা বলার পরেও গম্ভীর দেখে রাখিরও রাগ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু রাগ করতে গিয়ে হেসে ফেলেই বলেছিল, আচ্ছা আমার কী আগে আরো দুপাঁচবার বিয়ে হয়েছে যে এত অভিজ্ঞতা–কোনো কিছুর ভুল হতে পারবে না?
তখন ঠাণ্ডা।
মনঃপূত নয় এমন কিছু করলেই অভিমান। নিজের খেয়ালখুশিতেই রাখি এমন অনেক কিছুই করে বসে। বেঁকের মাথায় স্কুল থেকে হয়ত দলের সঙ্গে সিনেমায় চলে গেল, নয়ত একেবারে সন্ধ্যার পর বেরিয়ে ফিরল কোথাও থেকে। ব্যস, মুখ ভার। ফলে আগের থেকে মানুষটাকে ঠাণ্ডা রাখার কৌশলও রপ্ত করেছে রাখি।…সেদিন সুলতাদি রমলাদি ধরল–কাল রবিবার, তাদের টাইগার হিলএ নিয়ে যেতে হবে। খরচ সব রাখির। এড়ানো গেল না। ঠিক হল খুব সকালে বেরুবে, বেলা দেড়টা দুটো নাগাদ ফিরে আসবে।
কথা দিয়ে আসার পর রাখির ভাবনা। মানুষটা সঙ্গে যাবে না জানা কথাই৷ রবিবারে প্রথমে ছাত্র পড়তে আসবে গুটিকয়েক, তারপর মাস্টাররা আসবে কেউ কেউ। তাদের চা-টা একদিন অবশ্য ছোকরা চাকরটাই দিতে পারবে, কিন্তু তাহলেও ছুটির দিনে সকাল থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত বাইরে কাটানো বাবুর সহজে বরদাস্ত হবে না। তার ওপর একটু অন্যরকম রান্নাবান্না করা হবে না বলে বেলা দুটো আড়াইটে পর্যন্ত হয়ত না খেয়েই বসে থাকবে।
অতএব উল্টো প্যাঁচ কষল রাখি। বাড়ি ফিরে মুখহাত ধুয়ে বিকেলেই মুখরোচক কিছু খাবার তৈরী করল। তারপর গুনগুন করে গান করতে করতে খাবারের ডিস সামনে এনে ধরল। সুবীরকান্ত বই-মুখে চিৎপাত হয়ে বিছানায় শয়ান। রাখি তার মুখে কিছুটা খাবার গুঁজে দিতে সে হাসিমুখেই উঠে বসল।
জলযোগ শেষ হতে টুকিটাকি কিছু কাজ করার জন্য বেরিয়ে এলো। ও লোকটা আবার বই নিয়ে শুয়ে পড়বে জানা কথাই। খানিক বাদে রাখি লঘুপায়ে ঘরে ফিরল আবার। পর্দটা টেনে দিয়ে সোজা শয্যায় তার পাশে বসে পড়ে বইটা হাত থেকে টেনে ফেলে দিল। তারপর আধ-বসা হয়েই তার বুকের ওপর বুক রেখে দুহাতে মাথাটা ধরে ঝাঁকালো একবার। তারপর একেবারে মুখের ওপর ঝুঁকে বলল, মাস্টারমশায়, আমার একটা আর্জি আছে।
এই গোছের বিস্মৃতি পেলে তখনকার মতো পড়াশুনার আশায় জলাঞ্জলি দিতে সুবীরকান্তর একটুও আপত্তি নেই। দুহাতে তাকে বুকের সঙ্গে চেপে ধরে আর্জি যেন মঞ্জুরই করে ফেলল।–এই দিনের বেলাতেই?
–ধ্যেৎ, অসভ্য কোথাকার! হাত ছাড়াবার চেষ্টা।
–আচ্ছা বলো বলো।
–না, আগে তুমি কথা দাও!
–কথা দিলে শেষে যদি তুমি ফ্যাসাদে ফেলো আমাকে?
–ও, এই টান আর এই বিশ্বাস তোমার আমার ওপর?
–ছাড়ো
ছদ্ম রাগে আবারও হাত ছাড়ানোর চেষ্টা।
–আচ্ছা, কথাই দিলাম। বলো।
কাল সকালে তুমি ছেলে পড়াবে না, আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবে?
–কোথায়? আঁতকে উঠল যেন।
টাইগার হিলএ। খুব সক্কালে উঠে যাব, বেলা একটা দুটোর মধ্যে ফিরে আসব। সুলতাদি রমলাদি এমন ধরেছে, আমি কিছুতে এড়াতে পারলুম না। ওরা ঠাট্টা করে, মুখে মুখ লাগিয়ে আর কতকাল কাটাবি, চার সাল তো হয়ে গেল!
এর পর রমলাদি-সুলতাদির সঙ্গে ওকে ছাড়াই টাইগার হিল ঘুরে আসার জন্যে পাল্টা অনুরোধ শোনার পালা। ছেলেগুলো সমস্ত সপ্তাহ এই একটা দিনের আশায়। বসে থাকে, কী করে যায় সুবীরকান্ত-আগে জানলেও না হয় কথা ছিল!
বেগতিক দেখলে রাখি এই গোছের কৌশলে ঘরের লোকের অভিমান ঠেকিয়ে রাখে।
কিন্তু ও যেমন স্বামীর মান-অভিমান সবলতা-দুর্বলতার সন্ধান পেয়েছে, স্বামীটিও যে ঠিক তেমনি করেই তার স্ত্রীর চরিত্রটি নানা খুঁটিনাটির ভিতর দিয়ে সকৌতুকে পর্যবেক্ষণ করে চলেছে–সে খবর রাখির জানা নেই।
না, এযাবৎ নিজের স্ত্রীর প্রতি সুবীরকান্ত বিরূপ কখনো হয়নি। বরং অনেক ব্যাপারে তার ছেলেমানুষি দুর্বলতা দেখে বেশ মজাই লেগেছে।…ব্যাপারে আধুনিক চটকের ওপর স্ত্রীটির অনুরাগ। প্রথমেই তার নাক ধরে টান দিয়েছিল, বলেছিল, আচ্ছা নামের সঙ্গে তুমি আবার একটা কান্ত জুড়েছ কেন? সুবীর চক্রবর্তী তো বেশ নাম।
ও হেসে জবাব দিয়েছে, কান্ত নাই বলে বোধহয় বাপ-মা নামের ওপর দিয়ে অভাবটুকু উশুল করতে চেয়েছে।
–এখন ছেটে দাও।
–ছাঁটতে রাজি নই, বরং নাম বদলে রাখিকান্ত হতে পারি।
বিয়ের পরেই বাপেরবাড়িতে দিনকয়েক রাখি ওকে সুবীর বলেই ডেকেছে। কিন্তু একদিন ওর মায়ের কানে যেতে সুবীরের সামনেই কষে ধমক।-ও কী বিচ্ছিরি! খবরদার নাম নিয়ে ডাকবি না!
-বা-রে! ও যে নাম ধরে ডাকে?
–ও ডাকুক, তুই ডাকবি না।
আপত্তি সত্ত্বেও মায়ের কথা ফেলতে পারেনি। এখন আর ডাকে না।
দার্জিলিংয়ে আসার দিনকয়েক বাদে হঠাৎ একদিন বলেছিল, আচ্ছা এত বড় স্কলার হয়েও তুমি আই, এ. এস. পরীক্ষা দিলে না কেন?
–দিলে কী হত?
–দিলে আই. এ. এস, হতে পারতে না? আমার বন্ধু সোমার আই. এ. এস. বর, কী বিরাট চাকরি করে এখন জানো?
ঠিক এই গোছের ছেলেমানুষি ধরনের কথা না হলে সুবীরকান্তর হয়ত খারাপই লাগত। হেসেই ফিরে জিজ্ঞাসা করেছে, কেন, কলেজের মাস্টার পছন্দ নয়?
-মাস্টার পছন্দ নয়, তোমাকে পছন্দ।…চেষ্টা করলে তুমি আই. এ. এস. হতে পারতে।
-তা হয়ত হতে পারতুম, কিন্তু এই রাখিকে পেতাম না।
-কেন?
–তখন আর দার্জিলিংয়ে আসতুম না, তোমার সঙ্গে দেখাও হত না। তাছাড়া আই. এ. এস. হলে হয়ত লোভ আরো বেড় যেত, রাজকন্যা আর অর্ধেক রাজত্ব খুঁজতাম।
যুক্তিটা অস্বীকার করেনি রাখি, মাথা নেড়ে বলেছে, তা সত্যি, কী খরচটাই করেছিল তোমার কাকা, আমাদের ঘর-বাড়ি বেচলেও অত হত না।
স্ত্রীর উঁচু দৃষ্টির আঘাত পরের এই ছেলেমানুষি উক্তির দরুণই একটুও লেগে থাকে না। রং মজাই লাগে শুনতে। গম্ভীর মুখে ও-কথার পর বলেছিল, ধরো। আই. এ. এস, অফিসার হয়ে, আর তোমার বদলে তোমার বন্ধু সোমার বরটি হয়ে, আমি দার্জিলিংয়ে বেড়াচ্ছি-তোমার দেখতে কেমন লাগত?
ভালো যে একটুও লাগত না সেটা তার মুখ দেখেই বোঝা গেছে। আর জবাবটা আরও ভালো লেগেছে।-ইস! এখানেই যখন বিয়ে লেখা, যেভাবে হোক ঠিক তোমার সঙ্গেই জুটে যেতাম আমি।
স্ত্রীর আর একটা স্বভাব লক্ষ্য করে মুখ ফুটে কিছু না বললেও মনে মনে এক-আধ সময় উতলা হয়েছে সুবীরকান্ত। সর্বদাই রাখির দৃষ্টি যেমন উঁচু দিকে, খরচের হাতও সেই রকমই খোলা। বিলেতি ধাঁচের নামী স্কুল, মাইনে ভালই। দ্বীরকান্ত সে টাকা হাতেও নেয়নি কখনো, বলেছে তোমার কাছেই থাক। কিন্তু থাকছে যা এই কমাস সে ভালো করেই দেখছে। সব মাসের শেষেই তার চিন্তা দেখেছে-হাতের টাকা-টুকি ফুরিয়ে গেল, কী-যে করি!
জিনিস দেখলেই তার কিনতে ইচ্ছে করে। মনের মত ঘর সাজায়, সুবীরকান্তর জন্যেও এটা-সেটা কেনে। আর নিজের জামা-কাপড় কেনা তো সব মাসেই লেগে আছে। মাইনের অর্ধেক টাকা দিয়ে হয়ত একখানা শাড়ি কিনে বসল। পরে-পরে তক্ষুনি আবার তাকে দেখানো চাই।-কেমন হয়েছে?
চোখ তুষ্ট হলেও টাকার অংকটা ভিতরে ভিতরে খচখচ করতেই থাকে সুবীরকার। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারে না। ফলে রসিকতা করতে হয়, গরিব মাস্টার–এই রাখিকে আমি রাখি কোথায়?
রাখি তাইতেই খুশি, কোনো প্যাঁচ-পোঁচের ধার ধারে না সে।
যাই হোক, আনন্দের মধ্যেই দিন কাটছিল সুবীরকান্তরও। মাসপাঁচেক বাদে তার মনের দরজায় আর এক বৈচিত্র্য এসে হানা দিল। শুকনো-মুখ-রাখি সেদিন ঘরে ঢুকেই বলল, হয়েছে কাজ, এবারে ঠিক গণ্ডগোল বেঁধেছে!
মুখ থেকে বই সরিয়ে সুবীরকান্ত জিজ্ঞাস করল, কিসের গণ্ডগোল?
-আবার কিসের, যা হয় তাই, আরো খুব আনন্দ করো–কতদিন বলেছি একটু সামলে-সুমলে চলো!
তবু বুঝতে সময় লেগেছে একটু। তারপর বোঝা গেছে যখন বই ফেলে আনন্দে একেবারে উঠে বসেছে।-সত্যি? তারপর মুখের দিকে চেয়ে হাসতে সুরু করেছে।
রাখি রাগ দেখাতে গিয়েও হেসে ফেলল।-তুমি তো মজা দেখবেই এখন, আমি ওদিকে চিন্তায় মরি!
-কিসের চিন্তা?
স্কুলে তো আর একবছর ধরে ছুটি দেবে না, কিছুদিন গেলেই মেয়েরা ঠিক টের পাবে। কী লজ্জার কথা হল বলো তো?
ছদ্ম গাম্ভীর্যে মাথা নেড়ে সায় দিল।–তহালে এক কাজ করো, স্কুলের চাকরি। ছেড়ে দাও।
-বলো কী, চাকরি ছেড়ে এখন থেকে আমি ঘরে বসে থাকব?
–তাহালে চোখ-কান বুজে স্কুল করতে থাকো।…তোমাদের স্কুলের টিচারদের বুঝি কারো ছেলেপুলে নেই!
-থাকবে না কেন, মেম-টিচারগুলোর তো এক-একজনের তিনটে-চারটে করে ছেলেপুলে, ওদের অত লজ্জাসরমের বালাই নেই!
সুবীরকান্ত আরো গম্ভার।–প্রথমবার বলেই তোমার লজ্জা, পরের বার থেকে আর তোমারও থাকবে না।
এবারে গাম্ভীর্যের আড়ালে কৌতুক লক্ষ্য করল রাখি। রাগতে গিয়ে আবার ও হেসে ফেলল।–ভালো হবে না বলছি, সখ দেখে আর বাঁচি না!
এই সমাচারের দিন-কয়েকের মধ্যে সুধারকান্তর এই বহু প্রত্যাশিত পদোন্নতির সংবাদ এলো। এই কলেজেই লেকচারার থেকে প্রফেসার হয়ে গেল সে। সেদিন। কলেজ থেকে ফিরেই আনন্দে আটখানা হয়ে রাখিকে খবরটা দিল সে। আর রাতে চুপি চুপি বলল, যে আসছে সে বিশেষ ভাগ্য নিয়েই আসছে, বুঝলে…নইলে উন্নতির আশা তো কবে থেকেই করছিলাম, এতদিনেই বা হল কেন?
শুনে রাখিও খুশি বটে, কিন্তু তার মনে তখন নানা চিন্তা।
এর পরের কতগুলো মাসে যথার্থই আনন্দের মধ্য কাটল সুবীরকান্তর। নিজের মনেই জীবনের একটা নতুন স্বাদ অনুভব করে সে। আলো-বাতাসও অন্যরকম মনে হয়। রাখিকেও কেমন নতুন মনে হয় তার। ওর সর্বশরীরে যেন নতুন ছদ, নতুন সুষমার ছোঁয়া লেগেছে। চেয়ে থাকে, চুরি করে দেখে। আবার ধরাও পড়ে। রাখি লজ্জা পেয়ে হেসে ফেলে।–কী দেখছ?
সুবীরকান্ত হাসে শুধু।
সময় এগিয়ে আসতে স্কুল থেকে রাখি. তিন মাসের ছুটি পেল। ভিতরে ভিতরে তার নানারকম ভয়-ভাবনা। তাই ও প্রস্তাব করল, এ সময়টা মায়ের কাছে গিয়ে থাকলে কেমন হয়! আপত্তি করা উচিত নয়। কিন্তু এবারে সুবীরকান্তই দুর্ভাবনার মধ্যে পড়ে গেল।–তিন মাসের জন্য? ও বাবা, আমি থাকব কী করে?
অসহায় মুখখানা দেখে তার হাসিই পেল।…মায়ের কাছে যেতে ইচ্ছে করছে। বটে, কিন্তু সেই সময় এই লোক কাছে থাকবে না ভেবে আবার ভয়-ভয়ও করছিল। অতএব এখানেই থাকা মনস্থ করল সে। তাছাড়া এখানে ভালো ডাক্তার আর সুব্যবস্থার আশ্বাসও বেশি। তার ওপর সুবীরকান্ত যখন বলল, মাকেই বরং মাসখানেকের জন্য এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবে–তখন অনেকখানি নিশ্চিন্ত।
.
মেয়ে হল।
আর তাতেই যেন সুবীরকান্ত বেশি খুশি। মাস-দেড়েক না যেতে কঁপা হাতে শাশুড়ীর হাত থেকে মেয়ে কোলে নিয়ে বসতে চেষ্টা করেছে। নড়তে-চড়তে ভয়, পাছে মেয়ের লাগে। বাপকে রাগাবার জন্যেই মেয়েটাকে কুচ্ছিত বলে রাখি। তার কারণ মেয়ের রং একটু চাপা হবে বলেই মনে হয়, কিন্তু মুখশ্রী সুন্দর। শাশুড়ীর সামনেই এই নিয়ে ঝগড়া। মেয়ের নাম নিয়েও। সুবীর প্রস্তাব করে রাখির মেয়ের নাম পাখি হোক। রাখি তক্ষুনি স-ঝঙ্কারে আপত্তি করে, হ্যাঁ বয়েসকালে শেষে উড়ে পালাক আর কী! এ সুবীর হাসে।–বয়েসকালে তো উড়ে পালাবেই। শাশুড়ীর অনুপস্থিতিতে সেদিন বলেছিল, উড়ে পালাবার সময় হলে ওকে পরামর্শ দেব দার্জিলিংয়ে জলাপাহাড়ে উঠে বসে থাকতে।
কিন্তু আরো মাসখানেক না যেতেই রাখি সত্যিকারের দুর্ভাবনার মধ্যে পড়ল। মা তখন জলপাইগুড়ি ফিরে গেছে। রাখি আবার স্কুলে যেতে শুরু করবে। ভাবছে। তিন মাসের পরে আরো দেড় মাসের আধা-মাইনের ছুটিও ফুরিয়ে এসেছে। মেয়ের জন্য সবে ভালো একটা আয়া রাখা হয়েছে। সব সুব্যবস্থার মধ্যে আচমকা। এই খবর।
সুবীরকান্ত কলকাতায় বদলির হুকুম-পত্র পেয়েছে। শুনে রাখি বিমূঢ় একেবারে।
–কি হবে তাহলে?
–কি আবার হবে, যাব!
–আর আমি?
–তুমিও যাবে!
এই নির্লিপ্ততা দেখে রাখি আরো অবাক যেন।–চাকরি ছেড়ে দেব?
সুবীরকান্ত হাসতে লাগল, তুমি কী ভেবেছ চিরকাল আমি এই দার্জিলিংয়েই থেকে যাব?
না, রাখি কিছুই ভাবেনি। সমূহ সমস্যাটাই তার কাছে বড়। সে জোর দিয়ে। বলল, এখন চাকরি ছাড়া কোনো কাজের কথা নয়, তুমি বদলি ক্যানসেল করার ব্যবস্থা করো।
-পাগল নাকি!
এই এক কথাতেই রাখি বুঝে নিয়েছে সেটা সম্ভব নয়, অথবা সম্ভব হলেও এই লোক সে-রকম তদবিরের ধার-কাছ দিয়েও যাবে না। গোড়াতে রাগই হয়ে গেছে। তার। আসলে সে চাকরি করে এটাই বোধহয় তার পছন্দ নয়–ঘরের মধ্যে মেয়ে। আগলে বসে থাকুক তাই চায়। এই অনুযোগের পরেও মানুষটার তাপ-উত্তাপ নেই, কেবল হাসে।
রাখি বলতে ছাড়ে না, এই তো মাইনে, চলবে কী করে?
সুবীরকান্ত যেন আরো মজা পায়।-এক-বেলা খাব, কী আর করা যাবে…এত বড় চাকরিটা তোমার! শেষে হেসেই বলে, তোমার এত ভাবনা কেন, কত লোকে বুড়ো বয়েসে প্রফেসার হয়েও চার-পাঁচটা ছেলেপুলে নিয়ে চালায়, আর একটা মেয়ে। নিয়ে আমাদের চলবে না? তাছাড়া কলকাতায় মেয়ে-স্কুল নেই? চাকরি করতে চাইলে তোমার এত বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটা চাকরি পাবে না সেখানে?
এই প্রথম একটু আশার কথা শুনল যেন। আর তারপর সুবীরকান্ত যে প্রস্তাব দিল, ভাবতে গেলে সেটা রোমাঞ্চকরই বটে। সুবীরকান্ত পরামর্শ দিল, একটা কাজ যদি করো তো দেখবে এই বদলিটা আমাদের কাছে আশীর্বাদই হয়েছে। কলকাতায় গিয়ে ঘরে বসে দুটো বছর পড়াশুনা করে এম. এ.-টা পাশ করে নাও। স্কুল ছেড়ে তখন কোন কলেজেই চাকরি পেয়ে যাবে…আর মেয়েটাও ততদিনে একটু বড় হবে।
বরাবর উঁচু দিকে দৃষ্টি রাখির, তাই শোনামাত্র উৎফুল্ল। কিন্তু পরক্ষণে নিজের ওপর অনাস্থা।-হ্যাঁ, এতকাল বাদে আবার আমি করব এম. এ. পাশ, তাহলেই হয়েছে!
মুখে বললেও এ সম্ভাবনাটা একটা বড়গোছের আশার মতই মনের কোণে লেগে থাকল। তবু যাবার আগে তার মন-খারাপ। খুঁতখুঁত করে বলল, এই মেয়েটাই অপয়া, আসতে না আসতে আমার চাকরিটা গেল!
.
কলকাতায় এসে জীবনের নতুন অধ্যায় শুরু। আড়াইখানা ছোট ঘরের ফ্ল্যাট নিয়েছে একটা। তারই ভাড়া এককাড়ি। গোড়ায় গোড়ায় রাখি আবার চিন্তা করেছে –চলবে কী করে?
–ঠিক চলবে, কিছু ভেবো না। সুবীরকান্তর সেই এক কথা।
চলে যাচ্ছে ঠিকই। কিন্তু রাখির মনে মনে বাসনা, আর একটু ভালো চললে ভালো হত। ভিতরে ভিতরে সেই ভালো দিনে পদার্পণের সঙ্কল্প নিয়েই এম, এ, পড়ার জন্য প্রস্তুত হল সে।
আলাপ-আলোচনা করে ইকনমিক্স-এ এম. এ. পড়া সাব্যস্ত হল। বি. এ.-তে এই বিষয়টা ভালই লাগত তার। এ ব্যাপারে সুবীরকান্তরও উৎসাহ কম নয়। বই-পত্র সংগ্রহ করে দিল। তার কলেজের ইকনমিক্স-এর এক তরুণ লেকচারারকে বাড়িতে এনে হাজির করল। সুদর্শনা ছাত্রী-বউদিকে সে যথাসাধ্য সাহায্য করবে সানন্দে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল।
সুবীরকান্ত বলল, খুব বিদ্বান ছেলে, যতখানি পারো আদায় করে নাও।
রাখি ধরেই নিয়েছে তার এম. এ. পাশের রাস্তা সুগম। মনের আনন্দে তাই ঠাট্টা করেছে, বেশি আদায় করতে গেলে সেও যাদি কিছু আদায় করতে চায়?
অরসিক স্ত্রীর কাছে সুবীরকান্তও নয়। পাল্টা ঠাট্টা করেছে, গুরু যখন, চাইলে কী আর করা যাবে…কিন্তু খুব গোপনে, আমি যেন জানতে না পারি।
রাখির ভালো পাশ করার ইচ্ছে, যত, ধৈর্য তত নয়! বেশি পড়াশুনার নামে তার হাঁপ ধরে যায়। বিশাল সমুদ্র সে পার হবে কী করে, বই-পত্র খুলে এক-একসময় গালে হাত দিয়ে তাই ভাবে। ভাবতে ভাবতে অসময়ে ঘুম পেয়ে যায়। তারই ঘরের লোক বিনা উদ্দেশ্যেও অত পড়ে কী করে সেটা তার কাছে এখন এক বিস্ময়। বইগুলো বোঝার মত ঠেকে। মন হালকা করার জন্যে বিকেলের শোযে দুজনের সিনেমার। টিকিট কেটে বসে। সুবীরকান্ত কখনো বিরক্ত হয়, কখনো হাসে।এভাবে চললেই পাশ করা হয়েছে আর কী!
রাখি রেগে যায়, না হয় না হবে, আর পারিনে বাপু, কেবল মাস্টারি! কখনো বলে, আমার দ্বারা কিছু হবে-টবে না, আমার জন্যে তুমি একটা স্কুল-মাস্টারিই দেখো।
সুবীরকান্ত সে-কথা কানে তোলে না। পড়ার তাগিদ দেয়। ফাঁক পেলেই রাখি মেয়ের ঘাড়ে দোষ চাপায়, ওর জন্যে পড়াশুনা হচ্ছে না। মেয়ের জন্যে ওদিকে সর্বক্ষণের ঝি আছে একটা। আর বাপের আদুরে মেয়ে, বাপকে দেখলেই তার কোলে চেপে বসে থাকে। তাই ওর জন্যে পড়া কেন হয় না সুবীরকান্ত ভেবে পায় না। তা ছাড়া ঠিকে-চাকর আছে একটা, দুবেলার রান্না আর বাড়ির কাজ সে-ই করে দিয়ে যায়। এসব ব্যবস্থার ফলে প্রতি মাসেই খরচের টানাটানি। কিন্তু পারতপক্ষে সুবীরকান্ত তা জানতে দেয় না।
দ্বিতীয় বছরের কয়েকটা মাস কেটে যেতে রাখি একদিন হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসল। পড়া কিছুই এগোয়নি, কী করে পরীক্ষা দেবে!
আর তখুনি ঘরের লোকের আরেক রূপ দেখল সে। প্রথমে বিরক্ত হয়ে হুকুম করল, সব কটা পেপারে শূন্য পেলেও গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে আসতে হবে। তারপর বলল, আচ্ছা তোমার পাশ-ফেলের দায় আমার। যা বলি তুমি শুধু তাই করে যাও, আর কিছু ভাবতে হবে না।
এরপর থেকে দেখা গেল, ইতিহাস বই ছেড়ে তার ইকনমিক্স বই নিয়ে পড়াশুনায় মগ্ন হয়েছে লোকটা। আর দুবেলা নিজেই তাকে পড়াতে বসে যায়। প্রথমে বাংলায় জলের মত করে বোঝায়, তারপর ইংরেজিতে। এক-একটা দুরূহ পরিচ্ছেদ যে এত সহজে শেষ হতে পারে তার যেন বিশ্বাস হয় না। পড়ানো হলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানাভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে, ঠিক হলে উত্তর লিখে রাখতে বলে। আগের কয়েক বছরের প্রশ্নপত্র এনে সেগুলির খুঁটিনাটি জবাব শেখায়–লেখায়। খবরের কাগজ থেকে অর্থনৈতিক প্রসঙ্গের কাটিং রেখে তাকে পাঁচবার করে পড়তে বলে, লিখতে বলে। সব লেখাই আবার ধৈর্য ধরে সংশোধন করে দেয়। এই তন্ময় গম্ভীর মানুষটাকে তখন যেন খুব কাছের কেউ বলে মনে হয় না তার।
নিজের অগোচরেই একটু একটু করে আস্থা ফিরছে রাখির। তাই শঙ্কার ভাবটা কমছে। সব থেকে বড় কথা, একটু দুশ্চিন্তা দেখলেই মানুষটা ধমকায় তাকে।–তোমাকে তো বলেছি, শূন্য পেলেও তোমার কোন দোষ হবে না–সব দায় আমার।
এ-কথা শুনলে মনের জোর কার না বাড়ে! তাই রাত্রে দুজনে মুখোমুখি আধশোয়া হয়ে পড়াশুনা চলে যখন, রাখির মাথায় এক-এক সময় দুষ্টুমি চেপে বসে। একেবারে বুকের কাছে এগিয়ে গেলেও এত তন্ময় যে খেয়াল করে না। রাখি তখন আচমকা দুহাতে জাপটে ধরে তাকে, গালে গাল চেপে বলে, তারপর?
ধ্যানভঙ্গ হয় তখন। সেদিন এমনি ব্যাপারের পর সুবীরকান্ত তাকে টেনে ধরে রেখে জবাব দিল, তারপর পরীক্ষা হয়ে গেলেই আর একবার নির্ঘাত তোমার নার্সিং। হোমে যাবার ব্যবস্থা!
ছিটকে সরে আসতে চেষ্টা করেছে রাখি।-খবরদার, কখখনো না।
আর ছেলেপুলে হবার ব্যাপারে রাখির বেজায় আপত্তি। বলে, একটাই বেঁচে থাক, পাখিকে ভালো করে মানুষ করো, আর বেশিতে কাজ নেই।
মেয়ের ডাক-নাম পাখিই আছে। সুবীরকান্ত হাসে। বলে দেখা যাবে।
পরদিন সকালেই আবার সেই পঠন আর পাঠনের তন্ময়তা।
বেশ নির্বিঘ্নে এম. এ পাশ করার পরেও রাখি ভোলেনি আসল কৃতিত্বটা কার। ভালই পাশ করেছে। মাঝামাঝির থেকেও একটু উঁচুর দিকের সেকেণ্ড ক্লাস। সেটুকুও আশার অতিরিক্ত। ফল যেদিন বেরুল রাখি সেদিন গম্ভীর মুখে সুবীরকান্তকে জিজ্ঞেস করেছিল, জীবনে বোধহয় এই পরীক্ষাটাই সব থেকে খারাপ হল, কেমন?
যেন সুবীরকান্তই পরীক্ষা দিয়েছে এবং পাশ করেছে। সে হেসে জবাব দিয়েছে, হ্যাঁ।
জীবনযাত্রার পট পরিবর্তন আসন্ন বলেই বোধহয় এমন দিনে একজনের সঙ্গে দেখা রাখির। সেদিন কী একটা ইংরেজী সিনেমা দেখতে গেছল তারা, তাদের সামনেই ঝকঝকে গাড়ি থেকে নামল একজোড়া মেয়ে-পুরুষ। মেয়েটি গোলগাল মোটাসোটা, পরনে দামী শাড়ি, গলায় আর হাতে দামী গয়না। পুরুষটি ফিটফাট বাঙালী সাহেব। গাড়ি থেকে দম্পতিটিকে নামতে দেখেই সিনেমা দেখার আকর্ষণ ভুলে রাখি হাঁ করে তাদের দিকে চেয়ে রইল। পাশ কাটিয়ে যাবার মুখে মহিলাটিও তাকে দেখে থমকে দাঁড়াল।
অস্ফুট বিস্ময়ে রাখি বলে উঠল, সোমা না?
–রাখি, তুই!
হলের সামনে দুটি রমণীর পুলকিত জড়াজড়ির দৃশ্য দেখল অনেকে। তাদের স্বামী দুটি পরস্পরকে দেখে নিল একবার।
রাখির সহপাঠিনী সেই সোমা আর তার আই. এ. এস. স্বামী রমেন্দ্র সরকার। বান্ধবীর হাত ঝাঁকিয়ে রাখি বলে উঠল, কী গোল হয়ে গেছিস রে তুই, আমি তো প্রথমে হকচকিয়ে গেছি! পরক্ষণে আই. এ. এস-এর দিকে তাকিয়ে দুহাত জুড়ে নমস্কার জানালো, চিনতে পারেন?
বিব্রত জিজ্ঞাসু নেত্রে স্ত্রীর দিকে তাকালো ভদ্রলোক।–সোমা সরকার বলল, চিনবে কী করে, বিয়ের সময় সেই তো একবার দেখেছে! পরিচয় করিয়ে দিল, আমার বন্ধু রাখি গাঙ্গুলি–ওমা, গাঙ্গুলি বলছি কেন! সুবীরান্তর দিকে চোখ আটকালো তার, পরক্ষণে রাখির দিকে ফিরল।–বল না, ইনি নিশ্চয়?
হাসিমুখেই মাথা নাড়ল রাখি।–প্রফেসর সুবীর চক্রবর্তী।
আর এক-দফা সৌজন্য বিনিময়। ওদিকে সিনেমায় দ্বিতীয় বেল বেজে গেছে। খুশির ব্যস্ততায় সোমা জিজ্ঞাসা করল, সিনেমা দেখবি তো? কোথায় সীট তোদের?
কোথায় সীট রাখি জানে না, তবু বিব্রত অভিব্যক্তি একটু। সুবীরকান্ত জবাব দিল, নীচে।
সোমাদের ওপরের সব থেকে সেরা সীট সন্দেহ নেই রাখির। কিন্তু সোমা কিছু খেয়াল না করেই বলল, শো শেষ হলে পালাবি না বলছি, এইখানে দাঁড়াবি–কতকাল বাদে দেখা!
এত দিন বাদে দেখা হওয়ার ফলে রাখিও খুশি কম নয়। কিন্তু সোমার সঙ্গে তার অবস্থার তারতম্যটা এভাবে স্পষ্ট না হয়ে উঠলে যেন আরো খুশি হত। এতদিন বাদে আজ আবার মনে হল, তার ভদ্রলোকও যদি আই এ. এস-টাই হতে পারত–ইতিহাসের মাস্টার হয়েও যে আনায়াসে এম. এ. ক্লাসের ইকনমিকস পড়াতে পারে–ইচ্ছে করলে সে অনেক কিছু হতে পারত!
সীটে বসে বিস্ময় প্রকাশ করল, সোমাটা কী বিষম মোটা হয়েছে, দিব্বি ছিপছিপে চেহারা ছিল!
একটা কথা ভেবে সুবীরকান্ত মনে মনে কৌতুক বোধ করছিল, পরিচয় দেবার সময় রাখি সুবীরকান্ত বলেনি, শুধু সুবীর চক্রবর্তী বলেছে। ওর কথা শুনে মৃদু জবাব দিল, তোমার মত তো আর মাস্টারের বউ নয়, আই. এ. এস-এর বউ-সুখে আছেন। …কিন্তু শো ভাঙলে মহিলা আবার তো চড়াও করবেন মনে হচ্ছে!
চাপা হেসে রাখি জবাব দিল, তোমার তাতে ভয়টা কী, সঙ্গে আমি আছি, ওর। বরও আছে।
শো ভাঙতে শুধু চড়াও করা নয়, কোনো ওজর-আপত্তিতে কান না দিয়ে সোমা সরকার একেবারে গাড়িতে টেনে তুলল তাদের। আই. এ. এস. সামনে ড্রাইভারের পাশে বসল, তারা তিনজন পিছনে।
হাসিমুখে সোমা সরকার সুবীরকান্তর উদ্দেশে বলল, আপনার স্ত্রী-টি মশাই কি যে দুষ্টু ছিল আপনার কোনো ধারণা নেই, আমাদের একেবারে নাজেহাল করে ছাড়ত!
সুবীরকান্ত মন্তব্য করল, স্বভাব এখনো খুব বদলায়নি।
সোমা সরকার হালকা সুরে চ্যালেঞ্জ করল, আপনাকে তো বেশ ভালো মানুষ মনে হচ্ছে, না বদলালে সামলান কী করে?
সামলাবার চেষ্টাও করি না, হাল ছেড়ে দিয়েছি।
সকলেই হেসে উঠল। এমন কী সামনে থেকে রমেন্দ্র সরকারও হাসিমুখে এদিকে তাকালো।
সোমা সরকার বলল, না সামলালেও আপনার স্ত্রী আগের থেকে ঢের বেশি সুন্দর হয়েছে এখন, বুঝলেন?
সুবীরকান্ত জবাব দিল, আমি সামান্য মাস্টার, এতেও আমার কিছুমাত্র হাতযশ নেই।
আবার একপ্রস্থ হাসি। রাখির কানের কাছে মুখ এনে সোমা সোচ্ছ্বাসে বলল, বেশ লোকটি তো রে তোর! তারপর তেমনি চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করল, চেহারাখানা। তো দিব্বি কচি রেখেছিস–ছেলেপুলে কী?
-একটা মেয়ে।
সোমা জোরেই বলে উঠল, মাত্র!
রাখি তার হাঁটুতে একটা চিমটি কেটে মুখ বন্ধ করতে চাইল। তারপর গলা। আরো খাটো করে জিজ্ঞাসা করল, তোর?
সোমা সরকার ছদ্ম-কোপে তার আই. এ. এস, স্বামীর দিকে তাকালো একবার। তারপর জবাব দিল, আমার এক গণ্ডা।
বলা বাহুল্য, যত নীচু স্বরেই তারা বাক্যালাপ করুক, সুবীরকান্তর কানে এসেছে সবই।
সোমার বাড়ি-ঘর দেখে দুচোখ জুড়িয়ে গেল রাখির। ছবির মত বাড়ি, চমৎকার আসবাব-পত্র, আর তেমনি পরিপাটি ব্যবস্থা সব-কিছুর। ওর ছেলেমেয়েগুলোও তেমনি ফুটফুটে সুন্দর। সুখের ঘরে রূপের বাসা। রাখির যেমন স্বভাব, নিজের অবস্থার তুলনামূলক চিত্রটা মনে আসছেই।
বাড়ি ফিরে রাত্রিতে বিছানায় গা এলিয়েও ওদের কথাই ভাবছিল। বলল, কী চমৎকার আছে সোমারা, তাই না?
কাছে এগিয়ে এসে সুবীরকান্ত সায় দিয়ে বলল, চমৎকার, কিন্তু ওদের তুলনায় আমি আর এত পিছিয়ে থাকতে রাজি নই!
রাখি উৎসুক নেত্রে তাকালো তার দিকে। ভাবল অবস্থা ফেরানোর কোনো মতলবের কথাই শুনবে।
–ওদের চারটে ছেলেপুলে, আমার মাত্র একটা থাকবে কেন?
–যাও! রাখি ঠেলে সরাতে চেষ্টা করেছে তাকে।–তোমার কেবল ওই চোখে পড়েছে! কার সঙ্গে কার তুলনা!
সত্যি কথাই বলেছে। কিন্তু সব সত্যি কথা সর্বদা ভালো লাগে না। শেষের। এই তুলনার উক্তিটুকু সুবীরকান্তর কানে খুব মিষ্টি লাগল না।
এরপর সোমা সরকার একদিন তাদের ফ্ল্যাটে এলো। রাখি তাকে কোথায় বসাবে, কতভাবে আপ্যায়ন করবে ভেবে পায় না। তার গাড়ি পাঠিয়ে ওকেও দুতিনদিন তার। বাড়িতে নিয়ে গেল।
সেদিন তাদের বাড়ি থেকে রাখি রীতিমত একটা উত্তেজনা নিয়ে ফিরল। একটা অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য যেন সেধে তার দোরগোড়ায় এসে হাজির হবার উপক্রম করেছে। এখন শেষ পর্যন্ত এলে হয়।
সুবীরকান্ত ব্যাপারটা শুনল। আই. এ. এস. রমেন্দ্র সরকার এখন ডিরেক্টর অফ সোস্যাল ওয়েলফেয়ার, অর্থাৎ এই বিভাগটির সর্বময়কর্তা। এম. এ. পাশ করে রাখি কলেজে চাকরির চেষ্টা করছে শুনে সে একটা আশাতীত প্রস্তাব দিয়েছে। তার বিভাগে অ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়েলফেয়ার অফিসার নেওয়া হবে একজন–স্যোসিওলজির এম. এ. চাই, ইকনমিক্সও চলতে পারে, কারণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ.-তে এই সাবজেক্ট নেই। অবশ্য এ চাকরি হওয়া খুব সহজ নয়, পরীক্ষা হবে, ইন্টারভিউ হবে, তারপর চাকরির প্রশ্ন। তবে রমেন্দ্র সরকার সহায় বলেই আশা। সে নিজেই বলেছে, যতটা সম্ভব চেষ্টা করবে। আর সোমা তাকে বলেছে, ওরা ওরকম হাতে রেখে বলে, শেষ পর্যন্ত চাকরি তোরই হবে জেনে রাখ।
আশ্চর্য, এমন একটা খবর শোনার পরেও লোকটা প্রায় নির্বিকার! খানিক চুপ করে থেকে মন্তব্য যা করল শুনে রাখির রাগ হবারই কথা। বলল, মেয়েদের পক্ষে এ বড় ঝামেলার চাকরি, তার থেকে কলেজই ভালো।
-বলো কী? গোড়াতেই গেজেটেড র্যাঙ্ক, কলেজে যেখানে শেষ এখানে প্রায় সেই মাইনের শুরু। এর ওপর কত প্রমোশন আছে–ওয়েলফেয়ার অফিসার তো হওয়া যাবেই, অ্যাসিস্টান্ট ডাইরেক্টার, ডেপুটি ডাইরেক্টার পর্যন্ত হওয়ার আশা আছে। তাছাড়া কলেজের চাকরি যে পাবই তারই বা ঠিক কী?
না পেলে স্কুলে তো পাবেই।
ঠাট্টা করছে কিনা রাখির প্রথমে সেই সন্দেহ হল। পরে রেগেই গেল।–তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে?
সুবীরকান্ত জবাব দিল না, চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে রইল শুধু।
এরপর দিনকতকের জন্যে আহার-নিদ্রা ঘুচে গেল রাখির।
দরখাস্ত করা হল। রোজই একবার করে সোমার ওখানে ছুটতে লাগল। লিখিত পরীক্ষার জন্য কীভাবে তৈরি হবে, ইন্টারভিউতেই বা কী ধরনের প্রশ্ন করা হয়ে থাকে, এ-সব ব্যাপারে তার কিছুই ধারণা নেই। সোমাকে বলে, পরীক্ষায় চিত্তির করে এলে আর এ বাড়িতে মুখ দেখাতে আসতে পারব না বলে দিলাম।
আর ওখানে যজ্ঞেশ্বর কাপুর নামে একজনের সঙ্গে সরকার আলাপ করিয়ে দিল। জয়েন্ট ডাইরেক্টার, রমেন্দ্র সরকারের ঠিক নীচের লোক। সোমা বলেছে, আপিসের সর্বকর্মে সেই নাকি বৃহস্পতি। বয়েস রমেন্দ্র সরকারের থেকে কিছু বেশি হবে। হাসি-খুশি দিলদরিয়া মানুষ। এখানে অনেককাল আছে, মোটামুটি ভালই বাংলা বলতে পারে। তুমি বলে। তুমিটা অন্তরঙ্গসূচক জানার পর থেকে একটু খাতির হলেই সে আর কাউকে আপনি করে বলে না।
রমেন্দ্র সরকারের সামনেই সোমার আব্দার, মিস্টার কাপুর, আমার বন্ধুকে কিন্তু নিতে হবে, নইলে আপনার সঙ্গে কথা বন্ধ।
কাপুর হেসেই ভয়ের কারুকার্য ফুটিয়েছে মুখে।–কী সর্বনাশ, তাহলে তো নিতেই হবে।
পরীক্ষায় কী ধরনের প্রশ্ন আশা সম্ভব সেটা কাপুরই লিখে দিয়েছে তাকে। সে-সব নিয়ে রাখি আবার ঘরের লোকের শরণাপন্ন হয়ছে। এত বড় একটা ব্যাপারে তার নির্লিপ্ততা দেখে সে মনে মনে বিরক্ত। কিন্তু এখন প্রয়োজনে তোয়াজ না করে। উপায় কী?
বড় চাকরি করার ঝোঁক এত প্রবল যে সুবীরকান্তও আর মুখ ফুটে বাধা দেয়নি। নিজে খেটে-খুটে আর বইপত্র ঘেঁটে সম্ভাব্য প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখে দিয়েছে। আর গলদঘর্ম হয়ে রাখি সে-সব কণ্ঠস্থ করেছে।
পরীক্ষা হয়ে গেল। রাখি অবাক, আসতে পারে বলে কাপুর যা লিখে দিয়েছিল, হুবহু সেই সবই এসেছে। তার বাইরে একটিও নয়। এর দিনকয়েক বাদে কাপুর লাফাতে লাফাতে এক বিকেলে আপিস-ফেরত বড়কর্তা অর্থাৎ সোমার বাড়ি এসে হাজির। রমেন্দ্র সরকার তখন টুরে। পরীক্ষার ফলাফল জানার আশায় রাখি প্রায়ই সোমার ওখানে যায়। সেদিনও গেছল। তাকে দেখামাত্র কাপুর হৈ-হৈ করে উঠল। –কনগ্রাচুলেশনস ম্যাডাম, কনগ্রাচুলেশনস্! তুমি তো একটি সাংঘাতিক মেয়ে দেখি, পরীক্ষার খাতায় কী কাণ্ড করেছ! সোমার দিকে ফিরল।-বুঝলে ম্যাডাম, তোমার বন্ধু একটি জিনিস, পরীক্ষার খাতায় যা-সব লিখেছে আমার বাবার সাধ্যি নেই সেরকম লেখে! অফিসাররা সব কাড়াকাড়ি করে ওর খাতা পড়েছে!
চাকরি? কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে এর পরেও চাকরি হবে না!
হাওয়ায় ভেসে বাড়ি ফিরেছে রাখি। এতবড় কৃতিত্বটা কার প্রাপ্য সেটা সে ভালই জানে। সুখবরটা তক্ষুনি ভাঙল না। খাওয়া-দাওয়ার পর লোকটা আবার বই নিয়ে শুয়ে পড়েছে। ইদানীং পড়াশুনা একটু বেড়েছে লক্ষ্য করেছে। বইখানা হাত থেকে টেনে নিয়ে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে রাখল, তারপর দুহাতে গলা জড়িয়ে ধরে যেন একটা সবল অধিকার ঘোষণা করল।
-কী ব্যাপার?
রাখি বলল, ব্যাপার গুরুতর। তোমার এবারের চাকরির পরীক্ষাটা খুব ভালো হয়েছে–একেবারে ফাস্ট!
সুবীরকান্ত কিছুটা নির্লিপ্ত সুরে জবাব দিল, তোমাকে ফার্স্ট করার দায়ে যারা প্রায় প্রশ্নপত্র চালান করেছে, তাদের মুখ রক্ষা হয়েছে বলো!
মনে মনে একটু লজ্জা পেলেও উৎফুল্ল মুখে রাখি বেশ জোর দিয়েই বলল, বেশ যাও, সকলেই তো আর তোমার মত আদর্শ নিয়ে বসে নেই–কি যে হচ্ছে সর্বত্র তুমি খবরও রাখো না।
-বুঝলাম। তোমার চাকরি হচ্ছে তাহলে!
–হচ্ছেই তো। ছদ্ম-কোপে রাখি চোখ পাকালো।-কেন, না হলে তুমি খুশি হও?
সুবারকান্ত হেসেই জবাব দিল, ঠিক বুঝছি না!
রাখি বলল, তুমি একটা স্বার্থপর, একটা ভালো চাকরি করবো তাও তোমার হ্য হয় না। মেয়েদের পোস্ট, আমি না পেলে আর কোনো মেয়েই পেতো এটা–তাহলে আমি কী দোষ করলাম!
সুবীরকান্ত অন্তরঙ্গ আকর্ষণে তাকে আগলে রেখে হেসেই জবাব দিল, দোষ কিছু নয়, বিয়ের পর থেকে তোমার বড় হবার ঝোঁক দেখে আমার ভয়।
-বারে, চাকরিই যখন করব, ছোট চাকরি করব কেন?
সুবীরকান্ত তক্ষুনি ফিরে প্রশ্ন করল, আমার চাকরিটা ছোট চাকরি, না?
এবারে রাখি লজ্জা পেল একটু।-তুমি তো তবু প্রোফেসার, তোমার মতো তো। হলার নই আমি, প্রোফেসার হতে হতে বুড়িয়ে যাব।
-তাহলে তোমার স্কুলের চাকরিটা ছোট চাকরি ছিল বলো?
–অত সব জানি না, বিচ্ছিরি চাকরি।
এই প্রসঙ্গ বাতিল করে দিয়ে মনের আনন্দে আরো নিবিড়ভাবে বক্ষলগ্ন হল। নে। কিন্তু মানুষটাকে কেমন যেন অন্যমনস্ক মনে হল তার।
.
জীবনের একটা ছোট বৃত্ত থেকে অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষিত একটা বড় বৃত্তে দার্পণ করল যেন রাখি। এই বৃত্তের রূপ আলাদা, রঙ আলাদা।
গোড়ায় গোড়ায় তার কাণ্ড দেখে সুবীরকান্ত হাসত। দুঘরের ফ্ল্যাটে আর চলছে, তিনঘরের ফ্ল্যাট একটা সংগ্রহ করতেই হল। ঘর হলেই হল না, তার যোগ্য সাজসজ্জা চাই। সোফা সেট এলো, তার সঙ্গে রং মিলিয়ে জানলা দরজার পর্দা এলো। টেলিফোন তো অফিস থেকেই মিলেছে। ছমাস না যেতে মাসিক কিস্তির ব্যবস্থায় ছোটখাটো একটা ফ্রীজও কিনে ফেলল সে।
মুখের হাসি আস্তে আস্তে কমে ব্যঙ্গোক্তি করেছিল, এবারে একটা গাড়ি চাই না?
–রোসো, আস্তে আস্তে সব চাই। তোমার কি, ভোলানাথ, কিছুই চাই না।
এ-সবের সঙ্গে তাল রেখে চাকরির মর্যাদা অনুযায়ী নিজের বেশবাসের ব্যবস্থা।
ছমাসের মধ্যে কম করে চারমাসের শেষের দিকেই বিব্রত মুখে রাখি এসে বললে, কিছু টাকা দিতে পারো, আমার হাতে যা ছিল ফুরিয়ে গেছে!
সুবীরকান্ত টাকা দেয়, কিন্তু টিপ্পনীও কাটে।–তুমি বড় চাকরি পাওয়াতে আমার কত সুবিধেই না হচ্ছে!
-বেশ যাও। সব যেন আমি নিজের জন্যে খরচ করছি। আর টাকাগুলোও ছাই কিভাবে যে খরচ হয়ে যায়–তা গোড়ায় গোড়ায় তো এরকম হবেই, একবার সব গোছানো হয়ে গেল তখন দেখো।
কিন্তু গোছানোর শেষ কোনো কালে হবে এমন ভরসা সুবীরকান্ত রাখে না।
বছর ঘুরতে পাখিকে নিয়ে তাদের মধ্যে ছোটখাট ঝগড়াই হয়ে গেল একটা। পাখি চার-এ পড়েছে, অতএব এখন ওকে কিন্ডারগার্টেনে না দিলেই নয়। নামজাদা এক মিশনারী স্কুলে ব্যবস্থা করল রাখি।
কিন্তু এ ব্যাপারে ওর বাপের বেয়াড়া গো দেখে মনে মনে রীতিমত বিরক্ত। তার সাফ কথা, ওর জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না–যখন সময় হবে, আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মত ও সাধারণ স্কুলেই পড়বে।
রাখি দেখে আসছে তার অনেক ব্যাপারে মানুষটা ইচ্ছে করেই আপত্তি করে। রেগে গিয়ে বলল, তাহলে বড় স্কুলগুলো আছে কী করতে?
-বড় স্কুলের কটা বাপ নিজে তার মেয়ের ভার নেয় আমি খবর রাখি না, আমার মেয়ের ভার আমি নিজে যখন নিয়েছি, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। কিন্তু তার পরেই হেসে যে কথা বলেছে, রাগ হবারই কথা। বলেছে, তেমার অসুবিধেটা কোথায় আমি বুঝি, মেয়ে তোমার কোনো নাম-করা বিলিতি স্কুলে পড়ছে না, লোকের কাছে সেটা বলতে তোমার মানহানি হবারই কথা।
ঠিক এমনি করেই একটা ঠাণ্ডা বিচ্ছিন্নতা দুজনের মধ্যে এগিয়ে আসছে ক্রমশ। রাখির মনে হয় বাড়িতে পা দিলেই সে যেন একটা সঙ্কীর্ণ পরিবেশের মধ্যে এসে পড়ে। বাইরেটা এর থেকে অনেক উদার, অনেক প্রশস্ত।
এদিকে তার অফিসের খাটুনিরও অন্ত নেই। কিন্তু তাতে বেশ একটা আনন্দ আছে, বৈচিত্র্য আছে। এক বছরের মধ্যেই চাকরিতে রীতিমত সুনাম রাখি চক্রবর্তীর। তার জন্যে পড়শুনা এবং পরিশ্রমও কম করেনি। চাইলড় ওয়েলফেয়ার, মেটারনিটি ওয়েলফেয়ার, নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের উন্নতি এবং শিক্ষার ব্যবস্থা, তাদের কারিগরী শিক্ষার মহড়া, স্বাস্থ্য, সমস্যা, সাংস্কৃতিক উন্নতি, স্পোর্টস, কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন–ইত্যাদির ব্যাপারে যে কত কত বই আর কত রিপোট পড়তে হয়েছে তাকে ঠিক নেই। এবারে আর সে কারো সাহায্যভিক্ষা করেনি, খেটে খেটে আর চোখ-কান খোলা রেখে নিজের ভিত নিজেই তৈরি করেছে।
ঘরের লোকের মেজাজ-পত্র তখনো অবশ্য অতটা অপ্রসন্ন দেখা যায়নি। বরং। বলেছে, কাজ যখন নিয়েছ, সৰ্বরকমে সে কাজের উপযুক্ত হওয়া ভালো।
কিন্তু অদৃশ্য বিচ্ছিন্নতাটা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল তারপরে। কাজের আঁটঘাট যখন বোঝা হয়ে গেছে, আর যখন সে নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে–আপিস থেকে সন্ধ্যে গড়িয়ে যায় প্রায়ই। সব-দিন যে কাজ থাকে এমন নয়। আপিসের শেষে মাঝে-মাঝেই উঁচুমহলের বৈঠক বসে, পরামর্শ হয়, আলাপ-আলোচনা হয়, কোনদিন বা নিছক আড়াই হয়। এগুলোও চাকরির অঙ্গ। তাছাড়া উঁচু মহলের এখানে সেখানে আনন্দ-সমাবেশ বা সাংস্কৃতিক ডাকও আছেই।
কিন্তু বাড়ি ফেরামাত্র একখানা গুরুগম্ভীর মুখ দেখতেই হবে। যেন কত অপরাধ করে বাড়ি ফিরল সে। তিনটে কথা জিজ্ঞাসা করলে একটার জবাব দেবে। গোড়ায়। গোড়ায় দেরিতে ফেরার কারণ বলত। এখন আর কিছু বলে না। হয় বই, নয় মেয়ে। নিয়ে আছে। আর ওর সঙ্গে আড়াআড়ি করেই যেন মেয়েটার স্বভাব অন্যরকম করে তুলছে। শুধু ওর জন্যেই এখন আয়া আছে একটা, কিন্তু বাপ বাড়ি থাকলে এক ঘণ্টাও এখন আর তার কাছে থাকতে চায় না মেয়েটা। নিজে হাতে তাকে খাওয়াবে, জামা পরাবে, অতবড় মেয়েকে সর্বক্ষণ কোলে বসিয়ে আদর দেবে, ঘুম পাড়াবে। মেয়েও তেমনি হয়ে উঠছে, পানের থেকে চুন খসলে বাবা বলে চিৎকার। মনের মতো কথা না বললে বা কখনো ধমক-ধামক করলে তাকে পর্যন্ত শাসায়, বাবাকে বলে দেব!
রাখির রাগ হয়ে যায় এক-একদিন, বলে, বল গে যা, তোর বাবা এসে মাথা কাটবে আমার! আদর দিয়ে দিয়ে মাথাখানা খাচ্ছে একেবারে।
ঝাঁঝটা সুবীরকান্তর কানে যায়। কিন্তু সে বলে না কিছু। মেয়েটা একটু-আধটু অসুখে ভোগে প্রায়ই, তাতেও ওর বাপের বাড়াবাড়ি রকমের ব্যস্ততা। সেদিন কাজের চাপই বেশি ছিল একটু, সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে দেখে মেয়েকে কোলে বসিয়ে তার বাবা দুধের গেলাস নিয়ে সাধ্য-সাধনা করছে–কিন্তু মেয়ে কিছুতে খাবে না। রাখি শাড়ি বদলে মুখহাত ধুয়ে এলো, চা খেল–দুধের গেলাস হাতে তখনো সেই সাধাসাধি চলেছে।
এই দেখে মেয়ের বাবাকেই ঝাঁঝিয়ে উঠল রাখি।–আদর দিয়ে দিয়ে কী করে তুলছ এখন দেখো! তার পরেই মেয়েকে শাসালো, এই মেয়ে, ভেবেছিল কী তুই? খাবি তো খা, নইলে বেরো এখান থেকে!
মায়ের দিকে চেয়ে মেয়ে পাল্টা চোখ পাকালো।-তুমি একটা পাজী!
সঙ্গে সঙ্গে বাপের কোল থেকে মেয়েকে টেনে তুলে একটু জোরেই হয়ত ঝাঁকুনি দিল রাখি।–কী বললি?
মেয়ে ভ্যা করে কেঁদে উঠল। তাই শুনে আয়া ঘরে ঢুকতে রাখি তাকেও ধমকে উঠল, মেয়েকে দুধ-টুধ খাইয়ে দেখেশুনে রাখো না কেন? সব সময় বাবুকে কষ্ট করতে হয় কেন? ২৭৬
জবাবদিহি না করে আয় কাঁদুনে মেয়েকে নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে প্রস্থান করল। দুধের গেলাস হাতে সুবীরকান্ত যে-ভাবে চেয়ে আছে তাতে রাগ হচ্ছে রাখির।–কী, মাকে পাজী বলতে শিখেছে, শাসন করে খুব অন্যায় করেছি?
-না। তবে এই কথাটা সে তোমার কাছ থেকেই শিখেছে। দিনের মধ্যে দুই একবার তুমিই ওকে পাজী বলো, আর কেউ বলে না!
উঠে জানালা দিয়ে গেলাসের সবটুকু দুধ বাইরে ফেলে দিয়ে শূন্য গেলাসটা টেবিলের ওপর রাখল।–মেয়েটা কাল থেকে সর্দিতে ভুগছে, আজ একটু জ্বর-জ্বরও হয়েছে–রোজ যা খায় সকাল থেকে এ পর্যন্ত তার অর্ধেকও খায়নি, এ-খবর তুমি রাখো?
গেলাসের দুধ ফেলে দিতে দেখে অপমানে রাখির মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠেছিল। শেষের কথা শুনে বিপরীত প্রতিক্রিয়া।–আমাকে তো বলোনি!
-আমি বলব, কেমন? তুমি মস্ত চাকরি করো, তাই মেয়ের অসুখের খবর তোমাকে আমার কাছ থেকে পেতে হবে? কোনা খবর যখন রাখার সময় নেই, তখন শাসন করারই বা দরকার কী? সবে খেতে শুরু করেছিল মেয়েটা–মধ্যে এসে তোমাকে এই মুর্তি দেখাতে কে বলেছিল?
ঘর ছেড়ে চলে গেল। রাখি অপ্রস্তুত হয়েছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে চাকরির খোটাটা বিধছে। পায়ে পায়ে মেয়ের কাছে এলো। পিঠে হাত দিয়ে দেখল, একটু ছাক-ছাক করছে বটে। আর ঢপটপে সর্দিটাও মিথ্যে নয়। মুখের দিকে একটু চেয়ে থেকে বলল, খাবি?
মায়ের গম্ভীর অথচ নমনীয় মুখ দেখে মেয়ে কৌতুক বোধ করল। আয়ার কোল থেকে মাথা নাড়ল, খাবে। রাখি দুধ ঢেলে নিতে এলো আবার। বই ফেলে তক্ষনি সুবীরকান্ত উঠে এলো–দুধ কী হবে?
–ও খাবে বলছে।
–খেতে হবে না, রেখে দাও–যখন খাওয়াবার দরকার হবে আমি খাওয়াব।
রাখির সমস্ত মুখ লাল হয়ে উঠেছে আবার। দুধের সসপ্যান হাতে রাখি তার দিকে ফিরে চেয়ে আছে।
দেখছ কী, তোমার কোনো ব্যবহারে ওইটুকু মেয়েকে আমি অবাক করতে চাই না। রেখে দাও, নয়তো ওই প্যানসুদ্ধ দুধ আমি রাস্তায় ঢেলে দেব!
ফিরে গিয়ে আবার বই নিয়ে বসল। রাখি স্তব্ধ খানিকক্ষণ। লোকটার গোঁ জানে, কিন্তু মেজাজ তার নিজেরও কম নয়। জীবনের যে ক্ষেত্রে এখন বিচরণ তার, তুচ্ছ। কারণে এ-রকম ঝগড়াবিবাদ রুচিতে ঘা লাগার মতো। দুধের সসপ্যান রেখে সোজা ওই ঘরেই এসে দাঁড়াল সে-ও।
–আমার সঙ্গে আজকাল তুমি এ-রকম ব্যবহার করছ কেন?
সুবীরকান্ত বই পড়ছে–পড়ছে। জবাব দিল না।
অনুচ্চ কিন্তু আরো কঠিন সুরে রাখি বলে উঠল, তোমার এ-রকম ব্যবহারের অর্থ কী আমি জানতে চাই।
–তাতে অশান্তি বাড়বে।
–অশান্তি আমি করছি কেমন, তুমি নিজে কিছু করছ না!
সুবীরকান্ত বই পড়ছে।
.
বিচ্ছিন্নতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল আরো বছরখানেক বাদে।
সহকারী ওয়েলফেয়ার অফিসার থেকে রাখি চক্রবর্তী ওয়েলফেয়ার অফিসার হয়ে বসল। কিন্তু প্রত্যাশিত উন্নতিটা একটু অপ্রত্যাশিত ভাবেই এগিয়ে এলো তার সামনে। কথা ছিল, এক বুড়ো অ্যাসিসট্যান্ট ডাইরেক্টর বছর দেড়েক বাদে রিটায়ার করলে ওয়েলফেয়ার অফিসার মণিমালা ঘোষ অ্যাসিট্যান্ট ডাইরেক্টার হবে আর মণিমালা ঘোষের জায়গাটি তখন রাখি চক্রবর্তী দখল করবে। কিন্তু রাতারাতি অবাক ব্যাপার। হল একটা, বলা নেই কওয়া নেই মণিমালা ঘোষ হঠাৎ নিজের ইচ্ছেয় একেবারে অন্য বিভাগে অন্য চাকরি নিয়ে চলে গেল।
এই নিয়ে অবশ্য কানাঘুষো হল একটু। উড়ো গুজব কানে এলো রাখি চক্রবর্তীর, মণিমালা নাকি জয়েন্ট ডাইরেক্টার যজ্ঞেশ্বর কাপুরের ওপরেই রাগ করে চলে গেল। রাখি অবশ্য এ গুজবে কান দেয়নি। কারণ দিলখোলা যজ্ঞেশ্বর কাপুরের ওপর রাগ কারো হতে পারে না। তার ওপর এ আপিসে এসে অবধি মণিমালার সঙ্গে একটু খাতিরই বরং বেশি দেখেছে। একেবারে নিম্নপর্যায়ের মানুষদের কিছু চটুল রটনাও কানে এসেছে তার, কিন্তু এ-সব উক্তিতে রাখি কখনো কান পাতে নি। কারণ কাপুরের সঙ্গে খাতির সকলেরই–সে যখন ম্যাডাম বলে সরাসরি কাঁধে হাত রাখত অথবা হাত ধরে ঝাঁকাতো–রাখির নিজের মুখও গোড়ায় গোড়ায় লাল হত, এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আর বলতে গেলে কাপুরের খাতির এখন সব থেকে বেশি তার সঙ্গেই। রাখি জানে, এই নিয়েও আড়ালে চোখ-টেপাটেপি করে কেউ কেউ আজকাল। কিন্তু এ-সব নিম্নস্তরের ব্যাপার কখনো গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি সে।
মণিমালা ঘোষ আই. এ. এস. ডাইরেক্টটার রমেন্দ্র সরকারের নিজের খুড়তুতো বোন। নিঃসন্তান, বিধবা। বছর সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ হবে বয়েস, রমেন্দ্র সরকারের থেকে বছর দেড়-দুইয়ের ছোট। কিন্তু রাখি বা সোমার থেকে অনেকটাই বড়। ওরা মণিদি বলে ডাকত তাকে। আর রাখির বেশ ভালো লাগত তাকে। বুদ্ধিমতী, মোটামুটি সুশ্রী মিষ্টি চেহারা।
সে এভাবে হুট করে চলে যেতে রাখি অবাক হয়েছিল সন্দেহ নেই। সোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কী ব্যাপার, মণিদি চলে গেল কেন?
সোমা ঠোঁট উল্টে জবাব দিল, কে জানে, মেজাজী মেয়ে, ভালো লাগল না চলে গেল। আমাকে শুনিয়ে গেল, দাদার আণ্ডারে আর চাকরি করার ইচ্ছে নেই। তারপরেই মুচকি হেসে সোমা বলল, ও বদলি হয়ে তোর তো কপাল খুলে গেল রে!
মিথ্যে নয়, কপাল খুলেছে বটে। এখন তো ওয়েলফেয়ার অফিসার, দেড় বছর বাদে ওই আধ-বুড়ো অ্যাসিট্যান্ট ডাইরেক্টর রিটায়ার করলে সেই পোস্টও অবধারিত সে-ই পাবে। কাপুর এ আশ্বাসও তাকে দিয়েই রেখেছে। সে জয়েন্ট ডাইরেক্টর বটে, কিন্তু এসব ব্যাপারে সমস্ত বিভাগটির সময়কর্তা বলতে গেলে সে-ই। মিনিস্টর থেকে শুরু করে সকলের সঙ্গেই তার দহরম-মহরম। সেদিক থেকে প্রতাপ তার ডাইরেক্টারের থেকেও বেশি। কিন্তু মানুষ হিসেবে এমনি মজার যে প্রতাপের দিকটা কখনো কোনা কারণে উগ্র হয়ে ওঠে না।
ভাগ্যের এ-হেন পরিবর্তনেও নির্বিকার শুধু ঘরের একজন। এই কারণে রাখির ভেতরটা এখন বিরক্তিতে ভরপুর। তার মনে মনে ধারণা, তার বড় চাকরির দরুণ। লোকটা তাকে ঈর্ষাই করে। আসলে তার নিজেরই পুরুষকারের অভাব। নইলে এত বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে কলেজের মাস্টারিতেই খুশি থাকে কী করে? একটু খাটলে ডক্টরেট অনায়াসে পেতে পারে! রাখি একবার সেকথা বলেও ছিল। জবাবে যে কথা তাকে শুনতে হয়েছিল তাও চাপা গাত্রদাহ ছাড়া আর কিছু নয়। সে বলেছিল, বড় চাকর করার পর আজকাল আমাকে নিয়েও বোধহয় একটু লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তোমর!
রাখির রাগই হয়েছে। জবাব না দিয়ে চলে গেছে। ঘরের লোক মস্ত লেক, সেটা যে সব স্ত্রীরই গর্বের কারণ, এটুকু বোঝার মত উদারতা পর্যন্ত যদি না থাকে, তার সঙ্গে তর্ক করে কী হবে?
এমনি করেই হালকা ব্যাপারগুলোও ঘোরালো হয়ে উঠছে। যেমন সেদিন–সর পর এক বড় হোটেলে কাপুর সেদিন ওদের ডিনারে ডেকেছিল। ওদের বলতে রমেন্দ্র সরকার, সোমা সরকার আর রাখি। মনে মনে খুশি হল, কারণ ডিনারটা তাই প্রমোশনের খাতিরে। কিন্তু কাপুরের সেটা মাথায় না এলে রাখিই বা বলে কী করে?
ডিনারে হাসিখুশির ব্যাপারটা একটু বেশিই গড়ালো। এ-ধরনের নিরিবিলি সমাবেশে রমেন্দ্র সরকার আর কাপুরকে ড্রিঙ্ক করতে রাখি আগেও দেখেছে। সেদিন কাএ প্রস্তাব করল, তাদের সম্মানে মহিলাদেরও একটু ড্রিঙ্ক করতে হবে। সোমা সানন্দে রাজি। ও একেবারে অনভ্যস্ত নয়, সেটা খানিক বাদেই বোঝা গেল। কিন্তু তরল খুশির ব্যাপারটা জমে উঠল রাখিকে নিয়ে। সে কিছুতে খাবে না, কাপুর খাওয়াবে তাকে। গেলাসের রঙিন পদার্থ সে খুব হালকা করে মিশিয়ে তারপর সেই থেকে অনুরোধ করে চলেছে। শেষে সোমা বলেছে, অত করে বলছে, খা না বাপু, এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না–এই তো আমি দুবার মেরে দিলাম!
শেষ পর্যন্ত নাচার হয়েই গেলাসের জলীয় বস্তু চোখ-কান বুজে এক নিঃশ্বাসে জঠরে চালান করে দিল রাখি। বিচ্ছিরি লাগল। তেতো-তেতো স্বাদ। গায়ে একটা ঝঙ্কার দিয়ে উঠতে সকলে হেসে উঠল।
ডিনারের পর রমেন্দ্র সরকার কাপুরের গাড়িতে তার সঙ্গে কোথায় তাদের একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখতে চলে গেল। সোমা তার গাড়িতে রাখিকে পৌঁছে দিতে এলো। রাখির ভেতরটা তখন আনন্দে ভরাট, ভারী হালকা লাগছে। কোনো দুর্যোগের ছায়া তার কল্পনাতেও নেই। অন্যথায় বাড়ির দরজায় নেমে সোমাকে হয়ত গাড়ি থেকেই বিদায় দিতে চেষ্টা করত।
দোতলার বসার ঘরে ঢুকতেই সুবীরকান্তর সঙ্গে দেখা। সোমা হেসে বলে উঠল, আজ কিন্তু আপনার স্ত্রীর চরিত্র খারাপ করে দিয়েছি আমরা…কাপুর ওকে ড্রিঙ্ক করিয়ে ছেড়েছে!
শোনা-মাত্র মুখখানা যা হয়ে গেল, ভিতরে ভিতরে রাখি যেন কেঁপে উঠল। সোমাও বলে উঠল, ভয় পেয়ে গেলেন নাকি! কিছু ঘাবড়াবেন না মশাই, ইট ওয়জ জস্ট স্পোর্ট, আমি ওর ডবল খেয়েছি!
নিষ্প্রাণ ঠাণ্ডা গলায় সুবীরকান্ত জবাব দিল, আপনার যা সহ্য হবে ওর তা সহ্য। হবে কি?
সোমা চোখ পাকালো, কেন, আপনার স্ত্রীটিকে আপনি কারো থেকে কম ভাবেন। নাকি?
-না, তবে নিজের থেকেও খুব বেশি ভাবার মতো মুশকিলে না পড়ে যাই!
তরল বস্তুর প্রতিক্রিয়ায় সোমার ভেতরটাও খুব হালকা। অন্যথায় এই গম্ভীর আচরণ মর্যাদায় লাগার কথা। হেসেই রাখির দিকে ফিরল, তোর ভদ্রলোক দেখি বেজায় পিউরিটান, মেজাজপত্র খুব ভালো দেখছি না। আজ পালাই, আর একদিন এসে তর্ক করব।
লজ্জায় রাখির মাথা কাটা যাচ্ছিল। তাকে বিদায় দিয়ে ঘরে এসেই ফেটে পড়ল। বলে উঠলো, আমার বন্ধু হলেও ও আমার ডাইরেক্টরের স্ত্রী, এটা তোমার মনে রাখা উচিত ছিল–তুমি ওর সঙ্গে এ ব্যবহার করলে কী বলে!
হাতের বই রেখে সুবীরকান্ত আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।–কী রকম ব্যবহার করতে হবে, তোমরা স্পোর্ট করে মদ খেয়ে এসেছ সেই আনন্দে আটখানা হয়ে উঠব?
-কী বললে? স্পোর্ট কাকে বলে তুমি জানবে কী করে? নিজের কাছে এক মস্ত লেক হয়ে বসে আছ তুমি, বাইরের দুনিয়ায় কেউ তোমার আদর্শের কানাকড়িও দাম দেয় না, সেখানকার সভ্যতা ভব্যতা সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই–বুঝলে?
–ধারণা কার আছে, ওই কাপুরের? তাহলে তার কাছেই যাও!
–কী? কী বললে? দুপা এগিয়ে এলো সে।
–সামনে এসো না, ওইখানে দাঁড়াও। অনুচ্চ কিন্তু কঠিন এই স্বর শুনে রাখি থমকে আঁড়াল। তেমনি স্পষ্ট পুনরুক্তি সুবীরকান্তর। বললাম আমার দুনিয়ার আদর্শ আলাদা, সেটা যদি তোমার না পোষায়, তুমি অন্য ব্যবস্থা দেখতে পারো।
ভিতরের ঘরে ঢুকে গেল। সেখান থেকে মেয়ের ঘরে। মেয়ে রাতে আয়ার কাছে। ঘুমোয়–বাবা-মায়ের সঙ্গে একঘরে থাকা উচিত নয় বলে মাসছয়েক ধরে রাখিই এই ব্যবস্তা করেছিল। একটু বাদে মেয়ের ঘর থেকে আয়াকে বেরিয়ে আসতে দেখল। তারপরেই ওই লোককে শোবার ঘর থেকে নিজের বালিস নিয়ে যেতেও দেখল।
রাখির মাথায় আগুনই জ্বলছে। প্রতিদিনের এই সঙ্কীর্ণতার অত্যাচার যেন মুহূর্তের মধ্যে সহ্যের সীমা ছাড়াল। দুঘরের মাঝের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সে। দেখল। একট।..বাহুতে চোখ ঢেকে মেয়ের পাশে শুয়ে আছে। অপমানে রক্তবর্ণ হয়ে গেল রাখির মখ। ঠাস করে মাঝের দরজা টেনে বন্ধ করে দিল সে। এত জোরে যে ঘুমন্ত মেয়েটা চমকে উঠল।
থাকুক। দেখা যাক কদিন পরে থাকতে। আদর্শবান পুরুষের আর এক দিকও খুব ভালই জানা আছে তার। এ অপমানের জবাব সেও দিতে জানে।
দিন কাটতে লাগল। যে চিড়টা খেল সেটা আর জোড়া লাগল না। কিন্তু কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে উঠতে লাগল। বাক্যালাপটা প্রয়োজনের বাক্যালাপে এসে ঠেকল। রাখির। কাজের সুনাম যেমন বাড়ছে, ব্যস্ততাও বাড়ছে। দুদিন একদিনের জন্যে মাসে কয়েক দফা ট্যুরে বেরুতে হয়। বেশ আনন্দের মধ্যেই কাটে তখন। কখনো খোদ ডাইরেক্টর রমেন্দ্র সরকার সঙ্গে থাকে, কখনো বা জয়েন্ট ডাইরেক্টার যজ্ঞেশ্বর কাপুর।
কিন্তু ফিরে এলেই সেই নীরস গুরুগম্ভীর পরিবেশ। রাখির হাঁপ ধরে যায় এক এক সময়। কোনো সময় যদি মেয়ে বা মেয়ের বাপের শরীর খারাপ হয়, সে খবরও ঝি-চাকরের মুখে শুনতে হয়। কেউ বলে না তাকে। তাকে অপ্রস্তুত করার জন্যই যে বলে না, রাখি সেটা ভালই বুঝতে পারে। তবু যতটুকু সম্ভব নিজের কর্তব্য করে যেতে চেষ্টা করে। মেয়ের আব্দারে তার বাপের এখনো তার কাছেই শোয়া বহাল আছে।
একে একে প্রায় দুবছর ঘুরে গেল আরো। রাখির অক্লেশে প্রত্যাশিত উন্নতি হয়েছে আবার। সে এ্যাসিসট্যান্ট ডাইরেক্টার হয়েছে। কাপুর ট্যুরে। এই উপলক্ষে সোমা আর তার বর সেদিন ওদের ফ্ল্যাটে এসেছিল। রাখি আদর অভ্যর্থনা করেছে। তাদের। ইদানীংকালের মধ্যে রমেন্দ্র সরকার সস্ত্রীক আরো দিন-দুই তাদের ফ্ল্যাটে এসেছে। বলা বাহুল্য ডাইরেক্টর হিসাবে নয়, স্ত্রীর বন্ধুর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ধরেই। সুবীরকান্ত সে দুদিনের একদিনও বাড়ি ছিল না। এই দিনে ছিল, কারণ রাখি আগে। থেকেই তাকে বলে রেখেছিল। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও করেছিল।
সুবীরকান্ত হাসিমুখেই কথাবার্তা বলেছে তাদের সঙ্গে। তবু শুরুতেই রাখির মেজাজ বিগড়লো। তার মেয়েকে দেখে সোমা জিজ্ঞেস করেছিল, কোন স্কুলে পড়ো?
মেয়ে যে স্কুলের নাম করল সেটা যেন নতুন করে কানের পরদায় বিধল রাখির। তার ওপর সোমা বলল, একটা মাত্র মেয়ে তোর, একটা ভালো স্কুলে দিলি না কেন?
রাগ চেপে রাখি জবাব দিল, ওর বাবার আপত্তি।
সোমা হাসিমুখে সুবীরকান্তর দিকে তাকালো।-বাবা, আপনি এমন পিউরিটান যে মেয়েকে একটা ভালো স্কুলে দিতেও আপত্তি?
মেয়ের সামনে তার স্কুল সম্পর্কে এই উক্তি যে পছন্দ হবে না সেটা একমাত্র রাখিই জানে। সুবীরকান্ত ক্ষুদ্র জবাব দিল, এটাও খারাপ স্কুল নয়। মেয়েকে বলল, তুমি খেলা করো গে যাও।
সোমা হাসিমুখেই আবার বলল, কিন্তু আশা আর বাসা ছোট করতে নেই, আপনার স্ত্রীকে দিয়েই দেখলেন তো? বরাবর উঁচু আশা ছিল ওর–আপনার পাল্লায় পড়ে হতে যাচ্ছিল স্কুল-মাস্টার হয়ে বসল এ্যাসিট্যান্ট ডাইরেক্টর…কটা বছর গেলে ডেপুটি ডাইরেক্টরও হবেই।
রমেন্দ্র সরকার মাথা নেড়ে সায় দিল, ইয়েস, সী ইজ ভেরি ডিজারভিং!
ভিতরে ভিতরে রাখি উৎফুল্ল। ঘরের লোকের মুখখানাই দেখছে সে। রমেন্দ্র সরকারের কথা শুনে কান জুড়িয়েছে, আর সোমার কথাগুলো চমৎকার লেগেছে।
-আশা আর বাসা ছোট করতে নেই!
সুবীরকান্ত মৃদু হেসে সোমার দিকে তাকালো।–ডেপুটি ডাইরেক্টর হলেই আশা। আর বাসার শেষ?
সোমা জবাব দিয়েছে, আর কত চান মশাই?
-আমি চাইনে।…আশা আর বাসার মধ্যে খানিকটা সামঞ্জস্য না ঘটালে বিপদও হয়, সেই কথা বলছিলাম।
-কী রকম? সোমা উৎসুক।
–আশার থেকে বাসাটা বেশি বড় হয়ে গেলে খরচ বাড়ে, ঋণগ্রস্ত হতে হয়। আর, আর বাসার থেকে আশাটা খুব বেশি ছাড়িয়ে উঠলে অবজ্ঞায় যে বাসা আছে তাও ভাঙে।
লজিক! রমেন্দ্র সরকার তারিফ করে উঠল।
–ছাই লজিক! সোমা সরকার ছদ্ম কোপ দেখালো।–আমি লজিক পড়া মেয়ে, সব উপমাই অমন ভাঙাচোরা করা যায়।
.
রাখি চক্রবর্তী আর এক ধাপ ওপরে উঠেছে বলেই হয়ত সহিষ্ণুতা কমেছে আরো একটু। বাইরে তার মর্যাদা প্রতিপত্তি যত বাড়ছে, অন্দরের সহজ আলো-বাতাস যেন ততো বেশি সঙ্কীর্ণ ঠেকছে। চাকরির ব্যাপারে মিনিস্টারের সঙ্গে পর্যন্ত সহজ যোগাযোগ এখন (অবশ্য কাপুর আর রমেন্দ্র সরকারের কল্যাণেই সেটা আরো সহজ হয়েছে), ঘরের লোকের সেজন্য গর্ব বোধ করা দূরে থাক, তার রূঢ় অসহযোগ দিনকে দিন যেন আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।
কিন্তু রাখি আর অত কেয়ার করে না। কেউ যদি ইচ্ছে করে তফাতে সরে থাকে, সে কী করতে পারে? মাসের মধ্যে বার-দুই অন্তত এক এক দফায় চার পাঁচ দিন করে ট্যুর-প্রোগ্রাম আজকাল। কিন্তু ফিরে এসেও সেই গোমড়ামুখ দেখে মেজাজ চড়ে যায় তারও। আরো দু-তিন দফা ট্যুর-প্রোগ্রাম ফেলতে ইচ্ছে করে।
অনেক দিনের পুঞ্জীভূত মেঘ ফেটে ভেঙে চৌচির হয়ে পড়ল বুঝি সেদিন। কটা দিন রাখি বিশেষ ব্যস্ত ছিল। দুরের এক মফঃস্বল সহরে কম করে দশ-বারো দিনের ট্যুর-প্রোগ্রাম। বড় ব্যাপার। ছোট ছেলেমেয়েদের ফ্রী প্রাইমারি স্কুলের উদ্বোধন, তাদের শিক্ষার মহড়া, প্রসূতিসদনের উদ্বোধনী, জন্ম-নিয়ন্ত্রণ শিক্ষা সপ্তাহ পালন, ওয়েলফেয়ার একজিবিশন ইত্যাদি অনেক ব্যাপার। কটা দিন হিমসিম অবস্থা রাখির। বাড়িতে ফাইল-পত্র এনে রাত জেগে কাজ করতে হয়েছে, একসঙ্গে খাওয়াদাওয়ার ফুরসতও মেলেনি। তাছাড়া মেয়ের খপ্পরে না পড়লে সারাক্ষণ তো বই মুখে করেই আছে। রাখি চাকরকে বলে দিয়েছে, বাবুকে যেন সময়মতো খেতে দেওয়া হয়, তার সময়মত সে খেয়ে নেবে।
সেদিন ফাঁক পেয়ে একটু সকাল সকাল বাড়ি ফিরল। এসে দেখল কলেজের সেই অল্পবয়সী ইকনমিক্স-এর প্রোফেসারটি মেয়ের সঙ্গে গল্প করছে। এম. এ. পরীক্ষার সময় যে ভদ্রলোকটি তাকে খানিকটা সাহায্য করেছিল। তাকে দেখে বলল, দাদার জন্য বসে আছি, বাড়ি নেই শুনলাম। দুদিন কলেজ যাননি দেখে খবর নিতে এলাম, কী হল?
রাখি অবাক! দুদিন কলেজে যায়নি–ও জানেও না। তাছাড়া কলেজ পারতপক্ষে কখনো কামাই করে না। রাখি চাকরকে ডেকে তাড়াতাড়ি চা দিতে বলে বিস্ময় গোপন করতে চেষ্টা করল। ভদ্রলোকের নাম প্রতুল সোম। এ-কথা সে-কথার পর সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা বউদি, দাদা বদলির জন্য এরকম উঠে-পড়ে লেগেছেন কেন? আমরা জিজ্ঞেস করলে বলেন, এখানে শরীর টিকছে না।…কিন্তু যে-সব জায়গায় তিনি যেতে রাজি সে-সব কলকাতার থেকে কি এমন ভাল জায়গা?…আবার সরকারী চাকরি ছেড়ে বাইরের কোন কোন যুনিভার্সিটিতেও যেতে চেষ্টা করছেন শুনলাম, অবশ্য ওঁর মতো প্রোফেসার পেলে অনেকেই লুফে নেবে…কিন্তু ওঁর হঠাৎ এ-রকম ইচ্ছে। হল কেন?
রাখি নির্বাক বিমূঢ় খানিকক্ষণ। এমন একটা সংবাদ সে কল্পনাও করতে পারে না। তার মুখ দেখে প্রতুল সোমও প্রথমে অবাক, পরে অপ্রস্তুত। সে বলেই ফেলল, আপনি এ-সব জানেন না নাকি?
সহজ হবার চেষ্টায় প্রাণান্তকর ধকল। সমস্ত শক্তি দিয়ে হাসতে চেষ্টা করল রাখি। বলল, ঠিক এতটা জানি না…।
বেফাঁস কিছু বলে ফেলেছে বুঝে প্রতুল নোম আর অপেক্ষা না করে উঠে পালাল।
মাথায় আগুন জ্বলছে রাখির, সে অপেক্ষা করছে।
সন্ধ্যার একটু পরেই মানুষটা এলো টের পেল। সোজা তার শোয়ার ঘরে চলে। গেল। ওর ঘরে আসা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে।
খানিকটা সময় নিয়ে মাঝের দরজা দিয়ে রাখিই ও-ঘরে এসে দাঁড়াল। মেয়ে তখন বাপের বুকের ওপর উপুড় হয়ে কে এসেছিল সেই সমাচার জানাচ্ছে। তার বাবার গায়ে চাদর জড়ানো, শুকনো মুখ। কিন্তু আর লক্ষ্য করার ধৈর্য নেই রাখির। মেয়েকে বলল, ওদিকে আয়ার কাছে যাও।
মেয়ে আজকাল একটু ভয়ই করে তার মাকে। এই মুখের হুকুম শুনে তক্ষুনি চলে গেল। রাখি আরো একটু এগিয়ে এলো।-তুমি অন্য জায়গায় বদলির চেষ্টা করছ শুনলাম?
বদলির চেষ্টা নয়, আসলে সরকারী চাকরি ছেড়ে চলে যাবে কিনা, সম্প্রতি সেই চিন্তাই করছিল সে। জয়পুরের এক কলেজ থেকে তার আমন্ত্রণ যে এসেই গেছে, সেটা এ পর্যন্ত কারো কাছে বলেনি। এখনো বলল না। গায়ে চাদরটা আর একটু ভালো করে জড়িয়ে উঁচু বালিসে মাথা রাখল।
-হ্যাঁ।
-তা এ সামান্য খবরটা আমাকে বলোনি কেন, বাইরের লোকের কাছে বেশ ভালো-মতো অপমান করার জন্যে?
সুবীরকান্ত জবাব দিল না। ..
তীক্ষ্ণ কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রাখি।-আমাকে চাকরি ছাড়তে হবে?
–না।
–মেয়ে নিয়ে তুমি একা যাবে?
–হ্যাঁ।
চেয়ে আছে রাখি। মর্মান্তিক দেখাই দেখে নিচ্ছে যেন।–আশা বড় করেছি সেই মস্ত অপরাধে বাসা তাহলে ভাঙাই ঠিক করেছ তুমি?
সুবীরকান্ত নিরুত্তর।
দুচোখ ধক-ধক করে জ্বলছে রাখির। গলার স্বরেও এবার বুঝি আগুন ঝরল। –এত হিংসে তোমার ভেতরে ভেতরে! এত জ্বালা!
ধার কিন্তু পাণ্ডুর মুখে সুবীরকান্ত আস্তে আস্তে বসল। কঠিন স্বরে বলল, রাখি। আমার শরীর সুস্থ নয়, তুমি ও-ঘরে যাবে?
শরীর-মন কিছুই তোমার সুস্থ নয় সে তো অনেক দিন ধরেই দেখছি, ভিতরে এত বিকৃতি যার সে সুস্থ থাকবে কেমন করে? ও-ভাবে দেখছ কী, আজও তুমি মুখ বন্ধ করবে ভেবেছ? তুমি নীচ! তুমি অতি নীচ, অতি ছোট, অতি হীন, বুঝলে-বুঝলে?
তার মুখখানা ঝলসে দিয়েই এক ঝটকায় সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো।
হাঁপাচ্ছে। বুকের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে তখনো।
কবরের স্তব্ধতার মধ্যে কেটে গেল কয়েক ঘণ্টা। ও-ঘরের আলো অনেকক্ষণ। নিভে গেছে। মাঝের পর্দাটা ঝুলছে। রাখি নিজের ঘর থেকে বেরুলো একসময়। খাবার ঘরে আলো জ্বলছে। চাকরটা বসে আছে। তাকে দেখে উঠে এলো।-বাবু রাতে কী খাবেন বললেন না তো?
তার দিকে চেয়ে রাখি থমকালো একটু।–কী খাবেন মানে?
চাকর জানালো, আজ দুদিন বাবুর শরীর খারাপ, দুবেলাই দুধ-সাগু খাচ্ছেন –আজ কী খাবেন কিছুই বলেন নি।
কয়েক মুহূর্ত রাখি নির্বাক। তারপর চাকরকে বলল, আর অপেক্ষা না করে খেয়ে নিতে। তারও খিদে নেই বলে এলো।
.
পরদিন।
মেয়ে স্কুলে চলে গেছে। অফিসে বেরুবার আগে এক-রকম জোর করেই রাখি ঘরে ঢুকল।…চোখ বুজে শুয়ে আছে। টেবিলে ওষুধের শিশি একটা। তেমনি পড়ে আছে–এক দাগও খাওয়া হয়নি। কাল বিকেলে ডাক্তারের কাছে গেছল বোঝা গেল। সকালে টোস্ট পাঠিয়েছিল, তা তেমনি পড়ে আছে, শুধু চা খেয়েছে।
ফিরে তাকাতে দেখল তার দিকেই চেয়ে আছে। রাখির মানসিক যাতনা একটুও কমেনি। সমস্ত রাত বরং আরো বেশি জ্বলেছে। তবু এই মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ দার্জিলিংয়ের একবারের সামান্য অসুখের কথা মনে পড়ল। রাখি মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে কয়েকটা কথা বলেছিল।…এ মুখের সঙ্গে সেই মুখের মিল নেই একটুও।
জিজ্ঞাসা করল, তোমার কী অসুখ?
জবাব পেল না।
–আজ কলেজ যাবে?
নিরুত্তর।
–দুপুরে কী খাবে সে-কথা বলবে?
নির্বাক।
রাখি বেরিয়ে এলো। কাল বাদে পরশু অত বড় ট্যুর-প্রোগ্রাম, অফিসে অনেক কাজ। কিন্তু কাজ না থাকলেই বা কী করত? ও বাড়ি থাকলেই বরং না খেয়ে না দেয়ে ওই ভাবে বসে থেকে তাকে আক্কেল দেবে। ক্ষোভ আর একটা অসহ্য যাতনা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল।
এমনি স্তব্ধতার মধ্যেই সেই দিনটা গেল। পরের দিনও। সন্ধ্যা। প্রাণান্তকর বিমুখতা সত্ত্বেও পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকল।…বসে আছে। পাশে মেয়ে।
-কেমন আছ?
জবাব পেল। মেয়ে সামনে আছে বলেই।-ভালো।
ট্যুরে বেরোনোর খবর আগেই জানত। পাঁচ-ছদিন আগে রাখি বলে রেখেছিল। ভিতরে ভিতরে মানুষটা কোন ছুরি শানাচ্ছে তখনো জানা ছিল না। জিজ্ঞাসা করল, কাল আমার ট্যুর-প্রোগ্রাম, কী করব?
যাবে।
–ফিরতে আট-দশদিন দেরি হবে।
হবে।
বাইরে এসে কাজের চাপে সাময়িকভাবে যাতনাটা ভুলতে চেষ্টা করল রাখি। শুধু যাতনা নয়, সেই সঙ্গে বিদ্বেষ, ক্ষোভ-আবার কী একটা অজ্ঞাত ভয়ও…মানুষটার অভিসন্ধি জানার পর এতবড় একটা ব্যাপার ঘটে গেছে যখন, ভয়ের কিছু আছে। ভাবছে না। তবুও ভয়।
.
সমস্ত দিনে ফুরসত নেই বললেই চলে। বড় ব্যাপার। সোমাকে নিয়ে ডাইরেক্টর রমেন্দ্র সরকার এসেছে, জয়েন্ট ডাইরেক্টর কাপুর এসেছে, রাখি এসেছে, ওয়েলফেয়ার অফিসার এসেছে, আর আরো নীচের কর্মচারীরা যে কত এসেছে ঠিক নেই।
ওপরের দিকের ওরা মস্ত সরকারী বাংলোয় আছে-সস্ত্রীক রমেন্দ্র সরকার, কাপুর, রাখি আর ওয়েলফেয়ার অফিসার। রাতে কাপুরের ফুর্তির আড্ডা বসে। বোতলের রসদ সে কলকাতা থেকেই নিয়ে এসেছে। তাদের চারজনের আনন্দের আসর বসে। আনন্দ যে নেই সেটা বুঝতে না দেবার তাগিদেই রাখি যোগ দেয়। না এলে সোমা বা কাপুর গিয়ে ঘর থেকে ধরে নিয়ে আসে।
তাদের অনুরোধে গেলাসও হাতে তুলে নেয়। সমস্ত দিনের এত পরিশ্রমের পরেও রাতে ঘুম হতে চায় না। এই তরল জিনিস জঠরে গেলে চিন্তা-ভাবনাও কিছুটা ফিকে হয়ে যায়, ঘুমও একটু হয়। রাখি ভিতরের সমস্ত ক্ষোভ চিন্তা-ভাবনা যাতনা মুছে ফেলতেই চায়।
দশটা দিন কেটে গেল। রমেন্দ্র সরকার সোমা আর কাপুর কাল চলে যাবে। রাখির আরও দিন-দুই থাকা দরকার। মন না চাইলেও থেকেই যাবে।
রাতের আসর আজ একটু বেশিই জমেছে। রাখি গেলাস তেমন মুখে তুলছে না দেখে রমেন্দ্র সরকার নিজে পর্যন্ত দুই-একবার সাহায্য করতে এগিয়েছে। সোমার হাব-ভাবও অন্য দিন থেকে একটু বেশি খুশি-খুশি। বেশি খেয়েছে বলেই বোধহয়।
রাত মন্দ হল না। বরের শরীর খারাপ হবার ভয়ে সোমা একরকম জোর করেই রমেন্দ্র সরকারকে টেনে তুলে নিয়ে চলে গেল।
রাখিও উঠল।
কাপুর বাধা দিল, ম্যাডাম দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।
উঠে সোজা এগিয়ে গিয়ে ঘরের পুরু নীল পর্দার ওধারের দরজা দুটো টেনে দিয়ে সোজা তার কাছে ফিরে এলো। খুব কাছে। সঙ্গে সঙ্গে হাত দুটো তার দুই কাঁধে উঠে এলো।
-এ-ভাবে আর কত দিন চলবে? হোয়াই ওয়েস্ট টাইম?
-তার মানে? রাখি হতভম্ব। তার বোধশক্তি কয়েক নিমেষের জন্যে যেন বিলুপ্ত একেবারে।
-ও, ইউ নো ওয়েল! একটা জোরালো আকর্ষণ, পরমুহূর্তে পুরু দুই অধরের নিষ্পেষণে ঠোঁটদুটো যেন জ্বলেপুড়ে গেল রাখির। সর্বাঙ্গ অবশ, পায়ের নীচে মাটি দুলছে।
কয়েকটা মুহূর্ত। প্রাণপণে লোকটাকে ঠেলে সরালো সে। চকিতে বসন সংবরণ করে নিয়ে একটা চাপা আর্তনাদ করে উঠল প্রায়।–এ আপনি কী করছেন?
কাপুর থমকাল একটু। তারপর হেসেই আবার বলল, রাখি, লেটস কাম আউট –আমার ফ্লার্টিং ওয়াইফের সঙ্গে আমার বনছে না, তোমারও ওই রাফ হাজব্যাণ্ডের সঙ্গে বনছে না–সো লেট আস মেক অ্যারেজমেন্ট অ্যাণ্ড লেট দে গো টু হেল!
–এসব; এসব আপনাকে কে বলেছে? আমার কথা আপনাকে কে বলেছে? ক্রোধে আর সেই সঙ্গে এক অব্যক্ত যাতনায় রাখি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল।
আর তাই দেখেই কাপুর হকচকিয়ে গেল কেমন।-বোসো ম্যাডাম, আই অ্যাম স্থাউন্ড্রেল বাট নট মীন! আমাকে বুঝতে দাও। তুমি তোমার হাজব্যাণ্ডকে ভালবাসো?
রাখি অসহিষ্ণু জোরের সঙ্গে বলে উঠল, হ্যাঁ।
–সে তোমাকে ভালবাসে?
–বাসে।
কাপুর ধুপ করে সোফায় বসে পড়ল।–দেন আই অ্যাম এ ফুল অ্যাণ্ড হ্যাভ প্লেড ইন হার হ্যাঁণ্ডস এগেইন! শোনো ম্যাডাম, আমি একেবারে ভুল ধারণা থেকে এগিয়েছি–দ্যাট লেডী, সোমা সরকার, সী ইজ অ্যান ইনট্রিগিং গার্ল! নাও আই আণ্ডারস্ট্যাণ্ড এভরিথিং! –ওয়েলফেয়ার অফিসার মণিমালা ঘোষকে মনে আছে? ওদের আত্মীয়। সি লাইকড মি..পরিবারের দুর্নাম হবে সেই ভয়ে আমাদের মাঝখানে ওরা তোমাকে নিয়ে এলো। সোমা সরকার কত যে প্রশংসা করেছিল তোমার ঠিক নেই। আর আমারও সত্যি তোমাকে ভালো লাগতে শুরু করেছিল, সেটা বুঝেই মণিমালা সরে গেছে।
রাখি স্তব্ধ। কাপুর উঠে লম্বা ঘরটায় একবার পায়চারি করে তার হাত-কয়েক দূরে এসে দাঁড়াল।-ইদানীং সোমা সরকার তোমার স্বামীর সম্পর্কে আমার কাছে অজস্র নিন্দা করত, তাকে রোগ বলত, বলত বিয়ের পর থেকে কোনোদিন তুমি শান্তি পাওনি বলে তার ধারণা।-কেন বলত জানো? বিকজ হার হ্যাঁজব্যাণ্ড হ্যাঁজ স্টার্টেড লাইকিং ইউ, ইয়েস সী ক্যান স্মেল দ্যাট!–তাই সে এখন আমাকে দিয়ে তোমাকে ভালোমত আড়াল করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। আজ বিকেলেও আমাকে বার বার বলেছে, না এগোলে হবে কি করে, এতবড় সুযোগ পেয়েও এগোচ্ছ না কেন?
অদ্ভুত একটা হাসি দেখা গেল কাপুরের মুখে। সব ঝেড়ে ফেলেই যেন বলল, যাক, লেট এভরিওয়ান অফ আস একসেপটিং ইউ গো টু হেল! ক্যান ইউ ফরগিভ মি?
রাখি চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে। জবাব দিতে পারেনি।
পরদিন সন্ধ্যাতেই বাড়ি ফিরল রাখি। একটা দিনও আর দেরি করতে পারেনি। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, কী একটা ব্যাপারে যেন বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে। থেকে থেকে একটা দুর্যোগের ছায়া পড়ছে।
তাই ছুটে আসার তাড়া।
মেয়ে দৌড়ে এলো কাছে।-মা তুমি এসে গেছ! আমার কী খারাপ যে লাগছিল, ভাবছিলাম তোমার সঙ্গে যাবার আগে বুঝি দেখাই হল না!
বিষম চমকে উঠল রাখি। সত্রাসে তাকালো মেয়ের দিকে।–কোথায় যাবি?
-বারে, কাল যে আমরা জয়পুর চলে যাচ্ছি! বাবু বলেছে, কাল এই সময় ট্রেন।
রাখি বাকশক্তিরহিত। কোনরকমে দুপা এগিয়ে পাশের ঘরের পরদা সরালো। ঘরে কেউ নেই।
মেয়ে বলল, বাবা আরো কী সব কিনতে গেছে।
…নিজের ঘরের শয্যায় এসে বসল পাখি। নিস্পন্দ, কাঠ। রাখি পাশে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে কী যেন বলছে..বলছে বাবাকে আর সেই সঙ্গে ওকেও কলেজে নিয়ে গিয়ে কত খাতির করেছে, বাবাকে মোটা মোটা মালা পরিয়েছে, কত ভাল ভাল কথা বলেছে, তারপর কত কী খাইয়েছে তাদের!
নিষ্প্রাণ মূর্তির মত রাখি বসেই আছে।
সিঁড়িতে পায়ের শব্দ।…ওদিকের দরজা দিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে গেল। কিন্তু রাখির নড়ার শক্তি নেই। মেয়ের গলা কানে আসছে। মায়ের ফেরার খবর দিচ্ছে বাবাকে।
খানিক বাদে সুবীরকান্ত এ-ঘরে এলো। শরীর এখনো ভালো করে সারেনি বোধহয়। শুকনো মুখ। নির্লিপ্ত মুখে সামনের বিবর্ণ মূর্তির দিকে চেয়ে রইল একটু। তারপর ঠাণ্ডা গলায় বলল, ভাবনার কিছু নেই, তোমার অনেক ক্ষমতা, দুদিনেই ঠিক হয়ে যাবে। কাল যাচ্ছি আমরা, তুমি আজই আসবে ধরে নিয়েছিলাম, না এলে প্রতুলের কাছে চাবিটাবিগুলো রেখে যেতে হত…যাক, এই তোমার চাবি-পত্র–আর সব যেমন ছিল তেমনি আছে।
প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংবরণ করতে চেষ্টা করছে রাখি। অস্ফুট স্বর নির্গত হল গলা দিয়ে–যাচ্ছ কেন?
স্থির নেত্রে সুবীরকান্ত চেয়ে রইল একটু। জবাব দিল, যাচ্ছি, তোমার জীবনে এই নীচ ছোট হীন লোকের আর দরকার নেই বলে।
দরকার আছে।
দুচোখ ধারালো-হয়ে উঠছে সুবীরকান্তর।–আছে? বড় দুর্ভাগ্য আমার। তাহলেও যাচ্ছি, আমার জীবনেও তোমার প্রয়োজন ফুরিয়েছে বলে।
অসহিষ্ণু হাতে পর্দা ঠেলে নিজের ঘরে ঢুকে গেল।
পর্দাটা দুলে দুলে স্থির হল আবার।
রাতটা কীভাবে কাটল রাখি জানে না। ঘুমোয়নি, আবার জেগেও ছিল না। মাথার মধ্যে কী সব অজস্র হিজিবিজি ব্যাপার চলেছিল। সকাল হতে আর কিছু মনে নেই।
এক রাতের মধ্যে শরীরটা যেন পঙ্গু হয়ে গেছে। সমস্ত অস্তিত্বটাই যেন অনড় হয়ে গেছে। নড়তে-চড়তে কষ্ট। সকাল থেকে বসে আছে নিষ্প্রাণ মূর্তির মতো।
সাড়ে নটা বাজতে ধড়মড় করে উঠল।
অফিসে যাবে।
না খেয়েই বেরিয়ে গেল। অফিসে এলো। নিজের ঘরে বসে রইল চুপচাপ। একটা ফাইলও ওলটালো না। মাথার মধ্যে কী যেন সব তালগোল পাকাচ্ছে সেই থেকে। বেলা দুটো না বাজতে ভিতরে ভিতরে ওঠার তাড়া। ঘন ঘন ঘড়ি দেখল। কিন্তু জোর করে পাঁচটা পর্যন্ত বসেই থাকল। বাড়ি ফিরে কী করবে? কী করতে পারে রাখি? …চোখের সামনে মেয়ের হাত ধরে চলে যাচ্ছে, তাই দেখবে চেয়ে চেয়ে?
অন্যদিন অফিসের গাড়িতে বাড়ি ফেরে। আজ ট্রামে উঠল। তাতেও বেশ কিছুটা সময় চলে গেল। জায়গায় নামল। ট্রাম-স্টপের উল্টোদিকের রাস্তা ধরে আধ মিনিট হাঁটলে বাঁ-দিকে বাড়ি। ট্রাম-স্টপ থেকে বাড়িটা দেখা যায়।
রাখি রাস্তা পার আর হল না। ট্রাম-স্টপেই দাঁড়িয়ে রইল। বাড়িটার দিকে নিস্পলক চেয়ে রইল।
বিকেলের ছায়া ঘন হয়ে আসছে।
…বাড়ির দোরে একটা ট্যাক্সি দাঁড়াল। ও-মুখ করে। ওই ফাঁকা রাস্তা ধরে স্টেশনে যেতে সুবিধা। রাখির বুকের ওপর হাতুড়ির ঘা পড়ল। চাকরটা নেমে ভেতরে চলে গেল।
একটু বাদে মাল-পত্র তুলতে লাগল। বেশি কিছু নয়। মেয়ের হাত ধরে তার বাবা ট্যাক্সির সামনে এসে দাঁড়াল।
সমস্ত শক্তি একত্র করে রাখি দেখছে। নিঃশ্বাস রুদ্ধ।
তারা উঠল। ট্যাক্সি চলে গেল। ওই চাকাগুলো বুঝি রাখির বুকের ওপর দিয়েই। চলে গেল।
সামনে রাজ্যের অন্ধকার ধেয়ে আসছে। রাখি এবার তার আগেই বাড়ি পৌঁছুতে চায়। নইলে আর পারবে না। পায়ের নিচে মাটি দুলছে। পৃথিবী ঘুরছে।
…বাড়ি। সিঁড়ি ধরে দোতলা। দোতলায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সামনের দুটো শূন্য ঘর যেন হাঁ করে গিলতে এলো তাকে। মিনিটখানেক শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে রাখি আত্মরক্ষা করল।
তারপর পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকল।
মাথার মধ্যে আবার কী সব হিজিবিজি তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। রাখি তারও জট ছাড়াতে চেষ্টা করছে।…কী এমন হয়েছে? কিছু হয়নি। পৃথিবী রসাতলে যায়নি। সবই ঠিক আছে। জয়পুর আর কতদূর?…দার্জিলিংয়ে কবে যেন একটা লোক অসুখে পড়ে আনন্দ ছলছল চোখে বলেছিল–এত দিন তার কেউ ছিল না, এখন সব আছে। … আর ও নিজের হাতে খাবার তৈরি করলে সেই লোকটা ছোট ছেলের মত খুশি হত। অনেকদিন কিছু করা হয়নি। কিন্তু তাতে কী, দিন কী ফুরিয়ে গেল নাকি…জয়পুর কত আর দূর?
..কাপুর জিজ্ঞেস করেছিল, হাজব্যাণ্ড ওকে ভালবাসে কিনা, আর জিজ্ঞেস করেছিল, ও হাজব্যাণ্ডকে ভালবাসে কিনা। যেন এরকম সম্ভাবনার মতো ছেলেমানুষি। সম্পর্ক এটা। ঠোঁট দুটো বিষম জ্বালা করে উঠল হঠাৎ, সুরাযুক্ত দুটো অধরের স্পর্শ। তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে বেশ করে মুখটা ধুয়ে এলো।…সোমাটা হতচ্ছাড়ি একটা, দিল একটা ভালমানুষকে ক্ষেপিয়ে! কী না, ওর বর রাখিকে পছন্দ করতে শুরু করেছে! করলেই হল, অত সস্তা আর কী! জয়পুর যেন ভয়ানক দূর!
আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বিছানায় বসল।–কী যেন ভাবছিল। কী যেন ভাবা দরকার। কিন্তু আজ আর কিছু পারছে না। ভয়ানক ক্লান্ত। ঘুম পাচ্ছে। কাল ভাববে। পরশু ভাববে। ইচ্ছেমতো যে-কোন দিন ভাববে। আজ ঘুম পাচ্ছে–মোটা কথা, জয়পুর এমন কিছু দূর নয়!
ক্লান্ত অবসন্ন দেহটা রাখি শয্যায় এলিয়ে দিয়ে নির্জীবের মত চোখ বুজল। আজ আর কিছু ভাবতে পারছেই না। কাল ভাববে। পরশু ভাববে। ইচ্ছেমতো যে কোনদিন ভাববে। আজ রাখি ঘুমুবে।
আহুতি
সোমনাথ চাটুজ্যের কাছে আজও একে একে পাঁচ-ছ দফা লোক এলো। প্রত্যেকের কাঁধের ঝোলায় বিশ-পঁচিশখানা করে বই। বইগুলো তারা সোমনাথবাবুকে বুঝিয়ে দিয়ে বখশিশ নিয়ে চলে গেল! সোমনাথবাবুর থমথমে মুখ। বাড়ির চাকর সে বইগুলো তাঁর নির্দেশে ভিতরে নিয়ে গেল। ভিতরে মানে রান্নাঘরের সামনে ঢিবি করে রাখাল সেগুলো।
তিনদিন ধরে বাড়িতে লোকে বড় তাজ্জবকাণ্ড দেখছে কর্তার। বাড়ির লোক বলতে এখন ঠাকুর-চাকর, সোমনাথবাবুর গৃহিণী আর ছোট মেয়ে সুলেখা। আরো একটি জীব আছে, প্রভুর কাণ্ড দেখে সেও কম অবাক হবে না। সে কোন লোক নয়, সোমনাথবাবুর অ্যালসেসিয়ান উলফ। সব দেখেশুনে রগচটা এই জীবটিও হকচকিয়ে গেছে।
সব থেকে বেশি হতভম্ব সোমনাথবাবুর স্ত্রী শশীরানী। ডাক্তার ডাকার কথা কদিনই ভাবছেন। একটা ফোন করলেই ডাক্তার এসে পড়বে, কিন্তু শশীরানী ভরসা করে তাও ডাকতে পারছেন না। ডাক্তার এলে এই মানুষ আবার কোন মূর্তি ধরবে কে জানে!
সোমনাথবাবু হাসিখুশি মানুষ। কিন্তু কদিনের এই মুখ দেখলে কেউ বলবে না মানুষটা হাসতে জানে।
সোমনাথ চাটুজ্যে তেমনি গম্ভীরমুখে উঠলেন। চাকর যেখানে বইয়ের ঢিবি করেছে, পায়ে পায়ে সেখানে এলেন। বইগুলো দেখলেন একটু চেয়ে। ঝকঝকে বই, নতুনের গন্ধ লেগে আছে।
–কটা এলো?
চাকর তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল, আজও একশ ত্রিশ
পুরনো চৌকস চাকর। তার হিসেবে বিশ্বাস করা যায়।
বললেন, বোস, আরো খান-বিশ-পঁচিশ আসবে।
..প্রথম দিন আনা হয়েছিল পঁচাত্তরখানা। দ্বিতীয় দিনে একশ দশ। তৃতীয় দিনে একশ পঁচিশ। আজ আসবে কম করে একশ পঞ্চাশ। মনে মনে একটু হিসেব করে নিলেন সোমনাথবাবু। মোট দাঁড়াল চারশ পঞ্চাশ।…আরো দেড়শ কিনলে এ-যাত্রার কাজ শেষ।
ভিন্ন ভিন্ন বই নয়। একই বইয়ের কপি সব। উপন্যাস। নাম–অনুরাগ চক্র। এই বইয়ের ঢিবির সবগুলোই অনুরাগ চক্র। আজ চারদিন ধরে থাকে-থাকে খেপে খেপে কেবল অনুরাগ চক্রই আসছে সোমনাথবাবুর বাড়িতে। আরো দেড়শ এই বই-ই আসবে।
উপন্যাসখানার দাম আট টাকা। মোট ছশ বই যদি কিনতে পারেন সোমনাথবাবু, তাহলে দাম দাঁড়াল চার হাজার আটশ টাকা। বই যাদের দিয়ে কেনানো হচ্ছে তাদের মারফত কমিশন পাওয়া যাচ্ছে পঁচিশ পারসেন্ট। তার মানে বারোশ টাকা বাদ। তাহলে খরচা দাঁড়াল তিন হাজার ছশো। এ ছাড়া ওই লোকগুলোকে–যারা বই কিনে আনছে –তাদের বখশিশ দিতে হচ্ছে প্রত্যেককে দশটাকা করে।
যে দেড়শ বই আরো আসবে তার দাম বাদ বাকি সব টাকা সোমনাথবাবু দিয়েই দিয়েছেন।
এ বই অর্থাৎ অনুরাগ চক্রর লেখক সোমনাথ চাটুজ্যে নিজেই।
হ্যাঁ, এই চারদিন ধরে বিভিন্ন লোক মারফৎ নিজের বই-ই কিনে চলেছেন তিনি। কালকের মধ্যে নতুন চার-পাঁচজনকে দোকানে পাঠিয়ে আরো দেড়শ অন্তত কিনবেন।
বাইরে পরিচিত গলার হাঁক শোনা গেল। কার গলা চিনতে পারার সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা বিব্রত এবং বিরক্ত। যাঁর পদার্পণ তিনি যে, আসবেনই জানা কথা। ওই ভদ্রলোকের হন্তদন্ত হয়ে আসার মত একটা অস্ত্র সোমনাথ চাটুজ্যেই নিক্ষেপ করেছেন। তবু বিব্রত, তবু বিরক্ত।
– বাইরের ঘরে চেনা-গলার হাঁক শুনে আড়াল থেকে মনে মনে আশান্বিত কেউ যদি হয়ে থাকেন, তিনি শশীরানী। অন্যদিন হলে খুশিমুখে তিনিই বেরিয়ে আসতেন। আজ পারলেন না। আজ সঙ্কোচ। কিন্তু তা সত্ত্বেও আশা, ঘরের মানুষের এই মতির কিছু হদিশ মিলতে পারে এবার।
গাড়ি হাঁকড়ে যিনি এসে হাজির হয়েছেন তার নাম বিজয় ঘোষ। বাংলা দেশের এক নামজাদা প্রকাশক। তার অনুগ্রহ সরস্বতীর দপ্তরে প্রবেশের ছাড়পত্রের সামিল। অনেক মাঝারি লেখককেও প্রচারের মাধ্যমে প্রথম সারিতে এনে হাজির করেছেন তিনি, এ-দেশের লেখককুল তার প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু সোমনাথ চাটুজ্যের সম্পর্কে আজ অন্তত ঠিক একথা খাটে না। তিনি মাঝারি নন। একেবারে সামনের সারির একজন। বিজয় ঘোষের সঙ্গে তার বহুদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব। এই বন্ধুত্ব এখন অপর লেখক এবং প্রকাশকের চোখ টাটানোর মতো ফলপ্রসূ-এই শুধু বলা যেতে পারে।
সোমনাথ চাটুজ্যে বাইরের ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে বিজয় ঘোষ গলায় কাপড়ের খুটটা জড়িয়ে নিয়ে দুহাত জোড় করল।–কী অপরাধ বলো!
মিনমিন করে সোমনাথবাবু জবাব দিলেন, অপরাধ আবার কি, বোসো…।
গম্ভীর মুখে আসন নিয়ে বিজয় ঘোষ পকেট থেকে একটা রেজেস্ট্রি খাম বার করলেন।–আমি কি বিশ্বাস করব, এটা তুমিই আমাকে পাঠিয়েছ?
সোমনাথবাবু তেমনি মিনমিন করেই জবাব দিয়েছিলেন, হ্যাঁ ভাই…পাঠাতে হল। বিজয় ঘোষের গোল মুখের ওপর দৃষ্টি স্থির হল একটু।
-তোমাকে কে কী বলেছে?
–কেউ কিছু বলেনি।
–আমার থেকে কেউ বেশি টাকার টোপ ফেলেছে?
–না।
-আমি বাইশশ ছেপে দুচার হাজার ছেপেছি, এ-রকম রিপোর্ট কেউ দিয়েছে। তোমাকে?
– না।
সেদিন, যখন তুমি আমাকে টেলিফোন করেছিলে, আমি জানিয়েছিলাম দেড়মাসে দেড়হাজারের বেশি কপি বিক্রি হয়ে গেছে। হঠাৎ এই চারদিন ধরে বাকি কপিগুলো মুড়িমুড়কির মত বিক্রি হয়ে যাচ্ছে–আর দেড়শ বইও নেই। তবু আমি ঠিকমত তোমার বই বিক্রি করতে পারছি না–এ-কথা কেউ বলেছে?
-না, সে-সব কিছুই না।
ঈষৎ অসহিষ্ণু অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে বিজয় ঘোষ বলে উঠলেন, তাহলে আমার ওপর এই চিঠির বজ্রাঘাত কেন খুলে বলবে তো?…এই কদিনের বিক্রি দেখে রাতারাতি পরের এডিশন ছাপার জন্য আমি একসঙ্গে চারটে প্রেসের সঙ্গে ব্যবস্থা করে ফেলেছি-তার মধ্যে তোমার এই হুকুমজারি, এই বই আমি ছাপতে পারব না!
-ইয়ে, পরে সব তোমাকে বলবখন।
–এখনো পরে বলবে! তোমার এই চিঠির হুকুমই পাকা তাহলে?
–হুকুম আবার কী, বিশেষ দরকার হয়েছে…তাই।
–কিসের দরকার? টাকার?
–না।
–তাহলে আমাকে ছাড়ার?
সোমনাথ চাটুজ্জে নীরব।
–তা আমাকে ছেড়ে এ বই কাকে দিচ্ছ এখন, কে নিচ্ছে?
সোমনাথবাবু নিরুত্তর।
একটু চুপ করে থেকে বিজয় ঘোষ সখেদে বললেন, তুমি বই তুলে নিচ্ছ সে জন্যে দুঃখ নেই, কী হয়েছে বলছ না বলেই দুঃখ। তার মানে, এমন অপরাধ করেছি যার কোন ক্ষমা পর্যন্ত নেই, কি বলো?
ক্ষমার কথা শুনে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন সোমনাথ চাটুজ্যে।
কেন বার বার এসব কথা বলো, অপরাধ কারো যদি হয়ে থাকে এ দুনিয়ায়, আমারই হয়েছে, বুঝলে? বলতে বলতে আরো উত্তেজিত মুখে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। জানতে চাও এ বই কাকে দিচ্ছি? কে নিচ্ছে জানতে চাও? হঠাৎ এগিয়ে এসে হাত ধরে টানলেন, এসো, দেখবে এসো–
বিমূঢ় বিজয় ঘোষকে টেনে নিয়ে বারান্দা ছাড়িয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন তিনি।
শশীরানীর আড়াল ঘুচে যেতে তিনিও তটস্থ।
রান্নাঘরে চাকর সেই বড় উনুনটা ধরিয়েছে। সে-ই বইয়ের পাঁজা এক-একটা করে নিয়ে সজোরে টেনে ছিঁড়ে উনুনে দিচ্ছে। এক-একটা করে বই গনগনে উনুনে পুড়ছে আর সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে ছাই হয়ে যাচ্ছে।
বিষম হকচচিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি চাকরকে বাধা দিতে যাচ্ছিলেন বিজয় ঘোষ, নিজেই বাধা পেলেন। সোমনাথবাবু হাত ধরে থামালেন তাকে। বিরস কণ্ঠে বিড়বিড় করে বললেন, আমার হুকুমেই একাজ করছে। বই কাকে দিচ্ছি, কে নিচ্ছে দেখলে? চারদিন ধরে তোমার এত বই বিক্রি হচ্ছে কেন বুঝতে পারলে?
বিজয় ঘোষের দুচোখ ঠিকরে পড়ার দাখিল। এমন কাণ্ড তিনি এতকালের ব্যবসায়ী জীবনে আর দেখেননি। এই ধ্বংসযজ্ঞ আর তিনি সহ্য করতে পারলেন না। তার ওপর বিষম ঘাবড়ে গেছেন তিনি। লেখকের মাথা হঠাৎ সাম্প্রতিক খারাপ হয়ে গেছে, তাতে আর একটুও সন্দেহ নেই। এখন বই পোড়াতে পোড়াতে যদি বইয়ের প্রকাশকের মাথাও এমনি করে উনুনে গোঁজার রোখ চাপে–তাহলে? মনে হওয়া মাত্র তখনকার মত ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রস্থান করলেন তিনি। এরপর একেবারে ডাক্তার টাক্তার নিয়ে তবে বাড়িতে ঢোকা যেতে পারে।
মাথা যে সাজ্জাতিক রকমের খারাপ হয়েছে, শশীরানীরও তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। সুখের সংসারে কেন এরকম বিপর্যয় ঘটে গেল, তা তিনি কিছুটা আঁচ করতে পারেন। কিন্তু অনেকটাই দুর্বোধ্য এখনো।
শশীরানী প্রথমে ভেবেছিলেন, ওই হতভাগা ছেলে আর বড় মেয়েটা মুখে এ ভাবে চুনকালি দিল বলেই মাথাটা খারাপ হয়ে গেল। মানী লোক, চারদিকে কত নামডাক–মাথা খারাপই হবার কথা। দুঃখে ঘেন্নায় আজ কদিন ধরে তার নিজেরই তো বুকের ভেতরটা হু-হু করে জ্বলছে!
কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এর জন্যে ছোটও কম দায়ী নয়। বাপে আর ওই ছোট মেয়েতে সেদিন কি কাণ্ডই ঘটে গেল! দেখেশুনে ভয়ে-ত্রাসে অস্থির তিনি। অথচ বলতে গেলে ওই ছোট মেয়েই বাপের একেবারে চোখের মণি। তার ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বাপের এত আদর কেউ পায়নি। দুঃখের সংসারই তো ছিল এক-সময়। একটা মানুষ কলম চালিয়ে এতবড় বাড়ি করবে গাড়ি করবে, এত সম্মান প্রতিপত্তি হবে, একি স্বপ্নেও কখানো ভেবেছিলেন তিনি… ওই ছোট মেয়ে যেদিন কোলে এলো সেদিনই এক মস্ত সুখবর–কোন সিনেমা কোম্পানী স্বামীর একখানা গল্প কিনেছে, বেশ কয়েক হাজার টাকা ঘরে এসেছে।
সেই থেকে বাপের কাছে ছোট মেয়ের কদর। তারপর থেকে সত্যিই দিনে দিনে ভাগ্য ফিরেছে আর দেমাকী মেয়ের আদর বেড়েছে। অন্য ভাইবোন দুটো এ-জন্যে ওকে হিংসেই করে মনে মনে, শশীরানী বেশ বুঝতে পারেন।
আর ওই ছোট মেয়েও ছিল বাপ-অন্ত-প্রাণ। ওর বাপের সম্পর্কে কেউ কখনো একটু বিরূপ কিছু বলেছে কি, রক্তে নেই। লিখতে থাকলে সামনে ঘুরঘুর করেছে, কতক্ষণে বাবা লেখা ছেড়ে উঠবে আর ও তখন লেখা গোছগাছ করে রাখার নামে। ছাপার আগেই একদফা পড়ে নেবে। সেই মেয়ে কিনা এত লেখা-পড়া শিখে এম.এ পাস করে বাপের সঙ্গে এই ব্যবহার করল! সেই ব্যাপারের পর থেকেই বাড়িতে। এই পাগলের কাণ্ড চলেছে। মেয়ে দিনরাত দোতলার ঘরে বসে থাকলেও, নীচে কী ঘটছে কদিন ধরে সে কি জানে না? সব শোনার পরেও মেয়ে সেই আগের মত গুম হয়ে রইল তো রইলই। তার ওপর এই কদিনের মধ্যে একটা ডাক্তার পর্যন্ত ডাকল না। এখনো ওর রাগই বেশি! সবকটা স্বার্থপর, সবকটা অমানুষ।
সোমনাথ চাটুজ্যের এক ছেলে দুই মেয়ে। ছেলে সুদীপ, আর মেয়েরা শ্রীলেখা আর সুলেখা। সুদীপ টেনেটুনে বি.এ পাস করেছিল, তারপর সেই থেকে ভালো কিছু ব্যবসা করা যায় কিনা তাই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে চলেছে। চাকরিতে ঘেন্না তার।
শ্রীলেখা দুবার বি.এ. ফেল করে স্পষ্টই ঘোষণা করেছে, পড়াটড়া আর তার দ্বারা হবে না। কিন্তু সে চৌকস মেয়ে নয়, এমন কথা কেউ বলবে না। সপ্তাহে গোটা তিনেক ইংরেজি বাংলা সিনেমা একটা-দুটো থিয়েটার দেখে, আর কালচারাল নাটক টাটক করে তার ফুরসত নেই বললেই চলে। ছোট মেয়ে সুলেখা হায়ার সেকেণ্ডারিতে বেশ ভালো রেজাল্ট করেছিল, বি.এ-তেও খুবই ভালো, আর এম. এ-তে তো কথাই নেই-বাংলায় ফার্স্ট ক্লাস একেবারে। কাগজে যখন ওর ছবি বেরিয়েছিল, তখনকার মেয়ে সে সে-কথাও লেখা ছিল। এখন রিসার্চ করছে, তার জন্যে টাকাও পাচ্ছে।
শ্রীলেখা পড়ে না, একটা বই নিয়ে শুলেই- তার ঘুম পায়– যেটুকু পড়া হয়েছে। সেটুকুই আবার নতুন করে পড়তে হয়, নইলে কিছুই মনে থাকে না–আর সেই করতে গিয়ে আবার ঘুম। এই কারণে দীর্ঘদিন পর্যন্ত সোমনাথবাবুর মনে একটা খেদ ছিল। সেটা গেছে ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে উঠতে। তারা সকলেই বাপের লেখার ভক্ত। বিশেষ করে ছোট মেয়ের তো কথাই নেই। লাইন মুখস্থ বলে দিতে পারে অনেক বইয়ের। ওর মাকে বলে, বাবার দর্শনতত্ত্বর কত কথা যে আমি পরীক্ষার খাতায় মেরে দিই, ঠিক নেই!
অনেক আধুনিক চটকদার মাসিক আর সাপ্তাহিকপত্র ব্যক্তিগত ইন্টারভিউ নিয়ে লেখক-সমাচার ছাপায়। সেরকম লোক এলে সোমনাথবাবু সুলেখাকে পাঠিয়ে দেন। বলেন, আমার সম্পর্কে আমার থেকেও ও-ই ভালো জানে। বাপের সম্পর্কে ছোট মেয়ের বিবৃতিই ফলাও করে ছাপা হয়।
এমনি একটা ব্যাপারে প্রায় বছরখানেক আগে এই মেয়ের কাছ থেকেই প্রথম আঘাত পান সোমনাথবাবু। সুলেখা সবে এম. এ পরীক্ষা দিয়েছে, তখন নচের ঘরে এমনি এক কাগজের সম্পাদকের কাছে সুলেখাকে পাঠিয়ে ঘণ্টাখানেক বাদে দেখেন, সম্পাদকের কাছে বাপের সম্পর্কে ফলাও করে বলছে শ্রীলেখা। সুলেখা সেখানে নেই। পরে বড় মেয়ের কাছে যা শুনলেন তিনি, প্রায় অবিশ্বাস্য। সম্পাদককে নাকি সুলেখা বলে দিয়েছে, বাবার ইদানীং কালের লেখা সে পড়ে না, অতএব কিছু বলতেও পারবে না। অবাক হয়ে সম্পাদক জিজ্ঞাসা করেছে, কেন? ও জবাব দিয়েছে, ভালো লাগে না। দিদির ভালো লাগে, তাকে ডেকে দিচ্ছি।
শুনে রাগের থেকে সোমনাথবাবু অবাকই হয়েছেন বেশি। এই মেয়েটা যে এত বোকা তিনি কল্পনা করেননি! সাহিত্যে নতুন বাস্তবের বাতাস নিয়ে আসছেন তিনি। সে-বাস্তব অনেক সময় নির্মম, কুৎসিত, নগ্ন। কিন্তু উপায় কি, যে কালের যা! কালের এই রসদ যোগানোর ফল তো সকলেই দেখছে। তার শেষের চার-চারটে বই বাজারে হৈ-হৈ করে বিক্রি হচ্ছে। বিশেষ গোঁড়ামি যাঁদের, তারা সমালোচনার ফুল ফোঁটাচ্ছে। বটে, কিন্তু সাহিত্যে বিপ্লব আনতে হলে সকলকে খুশি করা যায় না। মেজরিটি যে খুশি, বইয়ের বিক্রিই তার প্রমাণ।
তারপর শেষের এই বই–অনুরাগ চক্র। বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে একখানা বই নিয়ে এত হৈ-চৈ বাংলা দেশে বোধহয় আর কোনো বই নিয়ে হয়নি। গোড়ারাও অবশ্য সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তাদের কাগজে তারা গালাগাল করেছে। তার উত্তরে সোমনাথবাবু নিজের খাতিরের কাগজে লিখেছেন, জীবনে সুন্দর আছে, কুৎসিত আছে, জীবনকে বাদ দিয়ে সাহিত্য হয় না। কুৎসিতকে অস্বীকার করা মানে জীবনকেই অস্বীকার করা।
এর জবাবে সেই গোঁড়াদের কাগজ ফলাও করে একজনের প্রশ্ন ছেপেছে। প্রশ্ন, সাহিত্যে-যাত্রা বলতে জীবনের কুৎসিত থেকে সুন্দরের দিকে যাত্রা বুঝব, না সুন্দর থেকে কুৎসিতের দিকে? জীবনের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, না আলো থেকে অন্ধকারের দিকে?
এই প্রশ্ন ফলাও করে ছাপা হয়েছে, তার কারণ ওই প্রশ্ন করেছে সুলেখা চট্টোপাধ্যায়–তার ছোট মেয়ে।
ছাপার অক্ষরে ওই নাম দেখে স্তব্ধ হয়ে ছিলেন সোমনাথ চাটুজ্যে। তারপর জুৎসই একটা জবাব লিখবেন ঠিক করেছিলেন।
কিন্তু সে-অবকাশ পেলেন না। তার আগেই বাড়িতে দ্বিতীয় বিভ্রাট আর এই দ্বিতীয় বিভ্রাটে মাথাই খারাপ হবার দাখিল সোমনাথবাবুর।
প্রথম বিভ্রাট গেছে মাসতিনেক আগে। তখনো অনুরাগ চক্র বেরোয়নি। বড় ছেলে সুদীপ পাড়াতে একটি বড়ঘরের কায়স্থ মেয়েকে নিয়ে ভেগে পড়ল। সেই সঙ্গে বাপের মাত্র হাজার পাঁচেক টাকা সঙ্গে নিয়েছে। লিখে রেখে গেছে তার বাবাকে, তিনি উদার; অসবর্ণ বিয়ে এখানেই হতে পারত, কিন্তু মেয়ের বাড়ির লোক ভয়ানক গোঁড়া বলেই আপাতত পালাতে হচ্ছে। স্ত্রীর কাছে ছেলেকে যথেচ্ছ গালাগাল করেই ক্ষান্ত হয়েছেন সোমনাথবাবু।
কিন্তু দ্বিতীয় বিভ্রাট তার চতুর্গুণ। বলা নেই, স্ত্রী হঠাৎ এক রাত্রে তাঁর লেখার ঘরে এসে হাউ-মাউ করে কেঁদে পড়লেন। তারপর ব্যাপার শুনে স্তম্ভিত তিনি।
বড় মেয়ে শ্রীলেখা অন্তঃস্বত্ত্বা। কিছুদিন ধরেই স্ত্রীর সন্দেহ হচ্ছিল। আজ যে করে হোক স্পষ্টই টের পেয়েছেন। আর বেগতিক দেখে শ্রীলেখাও স্বীকার করেছে। বলেছে, সেই ছেলে তাকে বিয়ে করবে, তাই আর দেরী না করে ব্যবস্থা। করা দরকার।
মাথার আগুন একরকম জল ঢেলেই নেবাতে হয়েছে সোমনাথবাবুকে। সেও এক কায়স্থের ছেলে। ছোটাছুটি করে আর হয়রানির একশেষ হয়ে দরকারী কাজ আগে সম্পন্ন করেছেন তিনি। সেই ছেলের সঙ্গে মেয়ের চুপিচুপি বিয়ে দিয়ে বিদায়। করেছেন তাকে। বাপ তার গলায় গামছা দিয়ে একাড়ি টাকা আদায় করেছে।
ধকল শেষ হতে মাত্র পাঁচ দিন আগে অগ্নিমূর্তি ধারণ করেছিলেন তিনি। বিষণ্ণ স্ত্রীকে বলেছিলেন, ছেলে আর বড় মেয়েকে ত্যাগ করলেন তিনি, আর তাদের মুখ দেখবেন না, কোন সম্পর্ক রাখবেন না–তার বাড়ি ঘর টাকাকড়ি সব তার ছোট মেয়ে পাবে–আর কেউ এক কপর্দকও পাবে না।
পাশের ঘর থেকে ছোট মেয়ে সুলেখা সটান তার সামনে এসে হাজির।-কেন পাবে না তারা? কেন তাদের ত্যাগ করবে? তারা কী দোষ করেছে?
প্রশ্ন ছেড়ে মেয়ের এই মূর্তি দেখে সোমনাথবাবু হতভম্ব। শশীরানীও। তীক্ষ্ণ চাপা স্বরে সুলেখা আবার বলে উঠল, জীবনের এই রাস্তায় গড়িয়ে তোমার চোখে এমন কী অন্যায় কাজ করেছে তারা? তারা যা করেছে সে-রকম ঘটনা তোমার এক-একটা বইয়ে অনেকবার করে ঘটেছে–আর শেষের বইটাতে তো কথাই নেই! তোমার অবাধ্য তো কেবল আমি হয়েছি, তাড়াতে যদি হয় আমাকেই তোমার তাড়ানো উচিত।
সোমনাথবাবু নির্বাক। হঠাৎ শশীরানী বলে উঠলেন, তোর কী মাথাখারাপ হয়ে গেল, মুখের ওপর এ-সব কী বলছিস্ তুই?
-ঠিকই বলছি মা। বাবা না তাড়ালেও এ বাড়িতে আর থাকার ইচ্ছে নেই আমার–আমি অন্য জায়গা খুঁজছি। কার মেয়ে বলতে পর্যন্ত এক-এক জায়গায় লজ্জায় পড়তে হয় আমাকে। সে-কথা থাক, কিন্তু বাবা কী বলে রাগ করে–এসব কথাই বা বলে কেন?
যেমন এসেছিল, তেমনি এক ঝটকায় সুলেখা আবার নিজের ঘরে চলে গেল।
এ-ঘরে শশীরানী নির্বাক, বিমূঢ়। আর সোমনাথ চাটুজ্যে বিবর্ণ, চিত্রার্পিত।
ঘৃণা
রোজই রাত নটা নাগাদ টার্মিনাস থেকে বাসে উঠি। ফেরার সময় তাই সপ্তাহের বেশির ভাগ দিন ওই লোকটার বাস জোটে। দোতলা স্টেট বাসের একতলার কণ্ডাক্টর সে।
প্রায়ই তার বাসে উঠি বলে মুখ-চেনা। তার কর্কশ স্বভাবের দরুনও মুখ-চেনা। উঁচু লম্বা চেহারা, চওড়া বুকের ছাতি। মাথায় আঁকড়া চুল। রুক্ষ চোয়াড়ে মুখ। গায়ের রং তামাটে, কালচে। পরনে ময়লা খাকি প্যান্ট, গায়ে বুকখোলা খাকি কোর্তা–ভিতরের বিবর্ণ তেল-চিটে গেঞ্জিটা চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক।
আমার মনে হত কণ্ডাক্টরি করতে হয় লোকটার সেই রাগ রাজ্যসুদ্ধ যাত্রীর ওপর। একদিন আমার সঙ্গেই লেগে গেছল একটু। টিকিট চাইতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনার কাছে দশটা টাকার চেঞ্জ হবে?
–না। খুচরো না নিয়ে ওঠেন কেন?
আমিও রুক্ষ জবাব দিলাম, খুচরো নিয়েই উঠেছি। দরকার ছিল বলে আছে। কিনা জিজ্ঞেস করেছিলাম। একটা সিকি তার হাতে দিলাম।
প্রায় শেষ প্রান্তের যাত্রী আমি, পঁচিশ পয়সাই ভাড়া। লোকটা টিকিট দিয়ে চলে গেল। একটু বাদেই ফিরে এসে হাত বাড়ালো, দিন।
আমি মাথা নাড়লাম।–দরকার নেই, আপনার ব্যবহারেই খুশি হয়েছি।
লোকটার অপ্রসন্ন দুচোখ আমার মুখের ওপর থমকালো। বলল, এ চাকরি করলে আর ব্যবহার মোলায়েম রাখা যায় না, বুঝলেন? ওই দেখুন, দেখুন বাস গড়ের মাঠ আর উনি গেটে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছেন! ও মশাই, বলি ভিতরেও হাওয়া খাওয়ার জায়গা আছে, উঠে আসুন!
টেরিলিন পরা গেটে-দাঁড়ানো শৌখিন তরুণটি মুখ লাল করে উঠে এসে বলল, ভদ্র ভাষায় কথা বলতে পারেন না?
লোকটা দুপা এগিয়ে তার ওপর দিয়ে গলা চড়ালো–অপর লোকের সুবিধে অসুবিধের কথা না ভেবে আপনি উঠেই গেটে গঁাট হয়ে দাঁড়ালেন–তার পরেও ভদ ভাষা যোগাতে পারলে তো ভাষার পণ্ডিত হয়ে বসতাম, বাসের কণ্ডাক্টরি করতে আসব কেন?
অনেকে হেসে উঠেছিল।
আর একদিন তো গোটাকতক ছোকরা যাত্রীর সঙ্গে হাতহাতি শুরু হয় আর কি। সামনের লেডিস সীট-এর দিকে গিসগিস ভিড়, পিছনের দিকটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা। লোকটা ঘেমে নেয়ে বারপাঁচেক ডেকে উঠেছে, পিছনে চলে আসুন না মশাইরা, সব ওদিকে ভিড় করছেন কেন?
কে কার কথা শোনে! শেষে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে লোকটা অল্পবয়সী কটা ছেলের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ওদিকে এত কী আনন্দ মশাই আপনাদের–ভিড়ের চোটে আধমরা হবার দাখিল, তবু ওখানেই দাঁড়িয়ে আনন্দ করা চাই–এদিকে সরে আসতে পারেন না?
ব্যস, এই থেকেই হাতাহাতি লাগে আর কী! গরম বচসার ফলে কণ্ডাক্টরের মুখ দিয়ে আরো যে কথা বেরুলো, তাই শুনে ওদিকের মহিলাদের মুখ লাল হবার কথা। ভিড়ের দরুন তাদের মুখ দেখতে পাইনি।
কণ্ডাক্টরের স্ব-পক্ষেও জনাকতক যাত্রী বচসায় যোগ দেবার ফলে সে-যাত্রা সত্যিকারের হাতহাতিটা হল না। টিকিট দেখতে চাওয়া, ঘণ্টা দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে লোকটার রুক্ষ ব্যবহার আমি আরো দিন-কয়েক লক্ষ্য করেছি। আমার ধারণা, এর দরুন লোকটাকে যাত্রীদের হাতে একদিন না একদিন নিগ্রহ ভোগ করতে হবে।
সকলের সেটা ছুটির দিন। আমাদের কাগজের অফিস খোলা। ঝমঝম বৃষ্টির ফলে বেরুতে সেদিন রাত দশটা হয়ে গেল। টার্মিনাসের বাসে উঠে দেখি সেই লোকটারই বাস।
বাস ফাঁকা। মাত্র পাঁচ-সাতজন লোক। কণ্ডাক্টর একেবারে পিছনের আগের সীটটাতে বসে নিবিষ্ট মনে সমবয়সী এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইছে। তাদের ঠিক পিছনের কোণের সীটটাতে আমি বসলাম। ফাঁকা বাস পেলে ওই সীটটাই আমার পছন্দ।
বসার পরেই যে কথা কানে এলো তাতে বোঝা গেল অনেক দিনের পুরনো বন্ধু তারা এবং অনেক দিন বাদে দেখা হয়েছে। আমি বসতে বসতে শুনলাম, ভদ্রলোক বলছে, তোর ভাইদের কারো কারো সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয়, তোর কথা জিজ্ঞেস করলে ভালো করে জবাবই দেয় না–প্রায় চার বচ্ছর বাদে দেখা হল তোর সঙ্গে, মনে করে একবার এলেও তো পারিস!
জবাবও কানে এলো।–এ ঘন্টার চাকরিতে জান কয়লা হয়ে গেল, সময় পাই কোথায় বল! তার ওপর ফাঁক পেলেই মুদি-দোকানে বসতে হয়, নইলে ভগ্নিপতিটির তো কুমীরের পেট-কড়া চোখ না রাখলে দেবে সব সাবাড়ে!
কণ্ডাক্টর আমার দিকে পিছন ফিরে বসে আছে। তার বন্ধুর মুখ সামনের দিকে। আমার মুখ বাইরের দিকে। বন্ধু জিজ্ঞেস করল, ভগ্নিপতির সঙ্গে শেয়ারে বিজনেস বুঝি?
–বিজনেস! কণ্ডাক্টরের গলায় একটু যেন কৌতুক ঝরল। পাঁচ হাত বাই পাঁচ হাত চালার নীচে কিছু মশলাপাতি, তেল, নুন, আলু, কয়েক হাঁড়ি গুড়, কিছু দড়ি দড়া আর কিছু আতপ চাল–প্রকাণ্ড বিজনেস!…তবু সময়ে ওটুকু করেছিলাম বলে গুষ্টিসুষ্ঠু উতরে গেলাম। হ্যাঁ ভগ্নিপতিই দেখছে এখন, চার আনা শেয়ার পায় আর কম করে চার আনা চুরি করে।
হুইসল বাজতে সে বসে বসেই হাত তুলে দড়ি টেনে ঘণ্টা বাজালো। গাড়ি ছেড়ে দিল। একবার ঘুরে বসে আমার টিকিটটা কেটে নিল। টিকিট কাটা হয়নি এমন যাত্রী আর কেউ আছে কিনা দেখল। তারপর বন্ধুর দিকে ফিরে বসল আবার।
এরপর বাসস্টপ এলে যন্ত্রচালিতের মতই ঘণ্টা দিচ্ছে, গেট দেখছে। দুই-একজন। যাত্রী নামছে, দুই-একজন উঠছে। আলাপের ফাঁকেও লোকটার সেদিকে চোখ আছে। উঠে টিকিট কেটে আবার বন্ধুর কাছে এসে বসছে।
এবারে তাদের অনুচ্চ মোট সংলাপটুকুর একটা চিত্র আঁকার বসনা।
বন্ধু : জমিটা তোর নিজের শুনলাম?
কণ্ডাক্টর : হুঃ, একেবারে জমিদার বলতে পারিস। কলকাতা থেকে সতের মাইল দূর, এই তো এগারোটার ডিউটি শেষ হলে রাত্রি দেড়টায় পৌঁছব।…তবু সেই হুজুগের সময় ধার-ধোর করে আড়াইশ টাকায় দুকাঠা জমি কিনে ফেলেছিলাম বলে ফুটপাথে থাকতে হচ্ছে না!
পাকা দালান তুলেছিস?
আটচালার ইমারং-ওই রক্ষা করতে প্রাণান্ত! কবে ফিরে দেখব সব সমান হয়ে গেছে!
কেন?
স্বাধীন হয়েছি না আমারা এখন? কথায় কথায় দিনেদুপুরে বুকে পিঠে ছুরি আর মাথায় ডাণ্ডা। আমাদের শালা মরণ-দশা, রামে মারলেও মারবে, রাবণে মারলেও মারবে। কতজন তো হুমকি দিয়ে রেখেছে–দেখে নেবে!
কেন?
কারণ দরকার হয় না, কারণ সব্বাই নিজেরাই তৈরী করে নেয়। মদ খাবার চাদা দিতে আপত্তি করলে তোমার পেট ফেঁসে যেতে পারে!
স্বল্পক্ষণের বিরতি। উঠে দুটো টিকিট কাটা, ঘণ্টা বাজানো এবং ফিরে এসে বসা।
বন্ধু : যাক, ছেলে-পুলে কী তোর বল দেখি?
কণ্ডাক্টর : একটা মেয়ে।
সেকি রে! প্রেম করে মেয়েটাকে মামার খপ্পর থেকে বার করে পালিয়ে নিয়ে গিয়ে কত কাণ্ড করে, বিয়ে–তারপর এতদিনে মাত্র একটা মেয়ে!
ওই সামলাতে প্রাণান্ত।
কেন, তোর পরের ভাই দুটো তো দাঁড়িয়ে গেছে!
দাঁড়িয়ে বুদ্ধিমানের মত সরে গেছে।…মেজটাকে আই-এ পরীক্ষার পর। স্টেনোগ্রাফি পাশ করিয়েছিলাম, আর সেজটাকে স্কুল ফাইন্যালের পরে টেকনিকাল স্কুলে ঢুকিয়েছিলাম। দুজনেই ভালো করছে এখন। ওদের মুখ চেয়ে আশায় আশায় কতদিন একবেলা খেয়ে কাটিয়েছি আমি আর বউ। যাক গে, ভাল থাক।
তার পরের জন?
চেষ্টাচরিত্র করে বি. কম. পড়াচ্ছি, সামনের বার পরীক্ষা দেবে।…ওটা বোকা, থাকলে থেকেও যেতে পারে। ওর বউদিকে খুব পছন্দ।
ছভাই তো তোরা, তার পরেও তো দুটো আছে।…তোর কাছেই থাকে, না?
হ্যাঁ, যাবে আর কোন চুলোয়!…ওরা ছোট, স্কুলে পড়ছে আর কু-সঙ্গে মিশছে। এক-একদিন ধরলে আধমরা করে ছাড়ি, কিন্তু দিনের হাওয়া যাবে কোথায়!
আচ্ছা, তুই ভাইদের জন্য এত করলি, মায়ের জন্যে যা করেছিলি সে তো নিজের চোখেই দেখেছি…মাঝখান থেকে শেষ বয়সেও তোর বাবাকে এত কষ্ট দিলি কেন?
তোকে কে বলল?
তোর পরের ভাই দুজনের মুখে শুনেছিলাম। খুব দুখ করছিল, শেষ সময়েও তুই নাকি অমানুষের মত ব্যবহার করেছিস।…কেন বল্ তো? শেষ পর্যন্ত তো মরেই গেল ভদ্রলোক
রুক্ষ জবাবটা ঠাস করে কানে লাগল আমার।-মরে তো সকলেই যাবে, কে আর চিরদিন বেঁচে থাকবে!
কলেজ স্ট্রীটের কাছে কিছু লোক উঠল। তাদের মধ্যে সাতজনের একটা গোটা পরিবারও আছে। স্বামী-স্ত্রী আর তেরো থেকে ছয়ের মধ্যে পাঁচটি ছেলেমেয়ে। তাদের পিছনে আরো পাঁচ-সাতজন লোক উঠেছে। ফাঁকা বাস, সকলেরই বসার জায়গা মিলেছে।
গাড়ি ছাড়ার ঘন্টি বাজিয়ে কণ্ডাক্টর টিকিট কাটতে এগলো। তারপর বচসা শুরু হল সেই পরিবারটির টিকিট সংগ্রহ করতে গিয়ে। মাঝবয়সী সেই ভদ্রলোকটি পাঁচখানা কালীঘাটের টিকিট কেটেছে।
–এদের টিকিট? কণ্ডাক্টর ছোট ছেলেমেয়ে দুটোকে দেখালো।
ভদ্রলোক বিস্ময়ের ভান করল, ওদের আবার টিকিট কী!
–ওদের তাহলে নামিয়ে দিই?
ফলে বাসসুদ্ধ লোকের কান খাড়া হল। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, ছেলেমেয়েগুলো রোগা-রোগা, ভদ্রলোক আর বউটাও রোগা। সকলেরই বেশ-বাসে দৈন্যের ছাপ।
ভদ্রলোক বলল, ওইটুকু ছেলেমেয়ে, নামিয়ে দেবেন কি-রকম!…ওদের তো কোনসময়ে টিকিট কাটি না।
-অন্যায় করেন। কাক্টর হাত বাড়ালো, আর দুটো টিকিটের দাম দিন।
নিরুপায় মুখ করে ভদ্রলোক পকেট থেকে আর একটা টিকিটের ভাড়া তার হাতে দিয়ে সুর পালটে বলল, আচ্ছা ওদের দুজনের জন্য আর একটা টিকিটি নিন..বুঝতেই তো পারছেন অসুবিধে হচ্ছে!
জবাবে অপ্রত্যাশিত রূঢ় ব্যবহার কণ্ডাক্টরের। বলল, অসুবিধে হলেও বাসে যখন উঠেছেন, আর একটা টিকিটের দাম দিতে হবে। দিন
এ রূঢ়তা অনেকের কানে বিধল। ছেলেমেয়েগুলো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে, বউটারও বিব্রত মুখ। একজন সহানুভূতিসম্পন্ন প্যাসেঞ্জার বলে উঠল, ভদ্রলোক মুখ ফুটে বলছেন, দিন না ছেড়ে
কণ্ডাক্টর তার দিকে ফিরল, তাহলে আপনি মুখ ফুটে বললে তো আপনার টিকিটও ছেড়ে দিতে হয়।
প্যাসেঞ্জারটির সঙ্গে সঙ্গে আরো দুজন বলে উঠল, খুব চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি ঝাড়ছেন যে মশাই,খুব ডিউটি দেখাচ্ছেন, কেমন?
-আমি দেখাচ্ছি না, আপনারাই আমার ডিউটিতে বাধা দিচ্ছেন।
এ-ধার থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠল, কেমন ডিউটিফুল আপনারা খুব জানা আছে মশাই!
কণ্ডাক্টরের তামাটে মুখ কঠিন। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে তেমনি হাত বাড়িয়ে বলল, কী, আপনি আর একখানা টিকিটের দাম দেবেন, না আমি গাড়ি থামিয়ে দেব?
বেগতিক দেখে এবারে লোকটি বিমর্ষমুখে আর একখানা টিকিটের দামও দিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে এধার-ওধার থেকে নানা ধরনের টীকা-টিপ্পনী শুরু হল। কণ্ডাক্টরের কানে তুলো, থমথমে মুখে টিকিট দিয়ে সে আবার তার বন্ধুর সামনে এসে দাঁড়াল।
লোকটার এই হৃদয়হীনতা কারোরই ভালো লাগেনি। তার বন্ধুটিরও খুব খুশি মুখ নয়।
চাপা রাগে চাপা গলায় কণ্ডাক্টর গরগর করে উঠল, বাসে উঠে টিকিটের পয়সা দেবার মুরোদ নেই, তার চার-পাঁচটা ছেলেমেয়ে–লজ্জাও করে না!
জ্বলন্ত চোখে ওই পরিবারটির দিকে একদফা অগ্নিবর্ষণ করল সে।
ঠিক সেই মুহূর্তে আমার চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা সরে গেল। কণ্ডাক্টরের বেশবাসের আড়ালে এই প্রথম সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা মানুষকে আমি দেখতে পাচ্ছি। …নিজের এতবড় সংসারের সমস্ত দায়িত্ব বহন করেও কেন সেই লোকটা শুধু তার বাপকে কষ্ট দিয়েছে, মৃত্যুর পরেও ক্ষমা করেনি–এই রুক্ষ মুখের দিকে চেয়ে যেন সেই জবাবও স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল।
চলো জঙ্গলে যাই
সকালে খানিকক্ষণ রেডিও শোনা অভ্যাস। তাই শুনছিলাম। চোখ অন্য-কাজে ব্যস্ত থাকলেও কান সজাগ ছিল। এই দিনে চোখ-কান-হাত-পা সব একই সঙ্গে যে বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করতে পারে না তার অগতি ব্যাহত হতে বাধ্য। আমার হাতে সিগারেট ছিল, চোখ দুটো সামনের বইয়ের দিকে ছিল, মনের একভাগ বইয়ের লেখকের দিকে আরেক ভাগ রেডিওর দিকে ছিল, আর মগজের কোষে-কোষে সিগারেট, বই, লেখক, রেডিও থেকে শুরু করে সমস্ত দিনের প্ল্যান-প্রোগ্রাম সবই আসা-যাওয়া করছিল। এই সব গুণ করায়ত্ত বলেই সিদ্ধির পথে আমার সহজ স্বচ্ছন্দ গতি। গেলবারে আমার সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক বন্ধুরা, সরকারী বে-সরকারী বহু পদস্থ শুভার্থীরা। আমাকে যখন মানপত্র দেন, তখন আমার বহু গুণের কথা উল্লেখ করে অনেকেই তারা সশ্রদ্ধ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তাদের সেই বিস্ময়ের উত্তরে আমি বিনীত জবাব দিয়েছিলাম, সবেতে সহিষ্ণু, সংযম, উদার দৃষ্টিভঙ্গি আর অতি মন্দের মধ্যেও ভালো দেখার চেষ্টা ছাড়া আমার আর কোনো গুণ নেই। শুধু এই কটি মিলিয়ে আমি যা–তাই।
মিথ্যে বলিনি বা অতিশয়োক্তি করিনি। মনেপ্রাণে এই তিন মন্ত্রের ওপরে নির্ভর করেই আমি দিনযাপন করে চলেছি।
সকালে রেডিও খুলি, কারণ প্রথম দিকে ভালো ভালো ঠাকুর-দেবতার গান থাকে কয়েকটা, যা শুনলে চিত্ত প্রসন্ন হয়, একটা শুচিশুদ্ধ ভাব জাগে মনে। তারপর রেডিওর খবরও খবরের কাগজের খবরের থেকে আমার ভালো লাগে। খবরের কাগজগুলো। সর্বদা দু-নৌকায় পা দিয়েই আছে, মানুষের চিন্তা বিভ্রান্ত করাই যেন তাদের কাজ। একই সঙ্গে প্রশংসা আর নিন্দা, স্তুতি আর কটুক্তি, আস্থা আর অনাস্থা–সব পাশাপাশি বিরাজ করছে। কিন্তু বেতারের খবরে উন্নতির প্রয়াস, অগ্রগতির চেষ্টা, সততা, নিষ্ঠা আর আশা-আশ্বাসের, একটা স্পষ্ট চিত্র মেলে। উজ্জ্বল সম্ভবনায় মন প্রসন্ন হয়।
বাড়িতে অবশ্য উঠতি বয়সের ছেলেছোকরা আছে আরো, নিজেদের তারা বেশ দিগগজই ভাবে। ভালো ভালো খবর শুনলেও তাদের মন ভরে না, তাদের চোখে অবিশ্বাস উঁকিঝুঁকি দেয়, ঠোঁটে অনেক সময় বাঁকা হাসি ফোটে, আর মনে মনে হয়ত বক্র শ্লেষও করে। কিন্তু ওদের এই বিরূপতা একটু রূঢ় শাসনেই আমি কাটিয়ে তুলতে চেষ্টা করছি। কিছুটা সফলও হয়েছি। এখন আর আমার সামনে অন্তত মুখ ফুটে কেউ কিছু বলে না।
আমি ওদের বলি, এত ধৈর্যশূন্য হবার কী আছে, এই তো সেদিন মাত্র স্বাধীন হলাম, শিশু দেশ আমাদের, এরই মধ্যে যা হয়েছে অনেক হয়েছে–ভোজবাজার ব্যাপার তো নয় যে রাতারাতি একেবারে প্রাচুর্যের বন্যা এসে যাবে!
জবাবে সব থেকে মুখের মত আমার স্ত্রীই একদিন মুখ-মচকে প্রতিবাদ করে বসেছিলেন, বলেছিলেন, তাও তো আঠের বছর হয়ে গেল দেশ স্বাধীন হয়েছে, শিশু আর কতকাল থাকবে?
সত্যিই আমার মনটা সেদিন খারাপ হয়ে গিয়েছিল–ঘরের স্ত্রী পর্যন্ত যদি মনে মনে অবিবেচক হন তাহলে কেমন লাগে? রাগ না করে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার ছেলের বয়েস কত?
আমতা আমতা করে জবাব দিলেন, উনিশ…
বললাম, তাকে তুমি কোন চোখে দেখো? মস্ত যোগ্য হয়েছে বলে তাকে তুমি ঠেলে রাস্তায় বার করে দিতে পারো? সেদিন পয়সা চুরি করেছিল বলছিলে, মস্ত নীতিবতী হয়ে, তাকে তুমি জেলে পাঠাওনি কেন? ও-বাড়ির ওই দুর্বল ছেলেটাকে, অমন ঠেঙিয়ে আধমরা করে আসার পরেও ওর তুমি একখানা হাতও ভেঙে দাওনি কেন? আপদে-বিপদে এত সন্তর্পণে তাকে তুমি আগলে রাখো কেন? এই সবেরই একমাত্র কারণ, আসলে ওকে তুমি শিশু ভাবো, এবং ঠিকই ভাবো। দেশটাকেও ঠিক এই চোখেই দেখা উচিত।
সেই মোক্ষম জবাবের পর স্ত্রীর মুখ বন্ধ হয়েছে।
যাক এসব কথা, আজ থেকেই আমার মেজাজ কিছুটা বিগড়ে দিয়েছে যে বস্তুটা, সেটা আমার হাতের এই বই। না পারছি ভালো করে রেডিওর খবরে মন দিতে, না পারছি বই হাতে নিয়ে আর কিছু ভাবতে। জুতোর ভিতর থেকে পায়ের তলায় ক্রমাগত যদি কিছু খচখচ করে বিধতে থাকে, আঘাত সামান্য হলেও কতক্ষণ আর সেটা বরদাস্ত করে নির্লিপ্ত থাকা যায়?
বইটার নাম চলো, জঙ্গলে যাই-জীবন-যন্ত্রণার প্রতীক এক আধুনিক কবির কাব্যসংকলন। চোখাচোখা বাক্যবাণ সাহিত্যের আওতায় আনার ফলে কবির একটু সস্তা নাম হয়েছিল। আমি নামই শুধু শুনেছিলাম, আগে তাঁর লেখা কিছু পড়িনি। পণ্ডশ্রম করার মত অত সময়ও নেই। কবির এই নবতম সংকলনটির প্রসঙ্গে পাঠকের একটু বেশি উচ্ছ্বাস প্রকট হবার ফলেই বইটা আমার হাতে এসেছে। আবার সুস্থ বুদ্ধি দু-চারজনের অনুরোধও এসেছে আমার কাছে, কবিতার বইটা পড়ে কাগজে আচ্ছা করে একটু সমালোচনা করুন তো–এ সব আপিন-সাহিত্য আর তো সহ্য হয় না।
সমালোচনার উদ্দেশ্য নিয়েই বইটা হাতে নিয়েছি, আর এ সপ্তাহে সমালোচনা প্রকাশ করতে হলে আজই এটা উল্টে-পাল্টে দেখে যা লেখার লিখে দিতে হবে। কিন্তু বইটা পড়তে পড়তে গায়ে যেন জল-বিছুটি লাগছে এক-একবার, ইচ্ছে হয়েছে। ছুঁড়ে ফেলে দিই। কিন্তু ছুঁড়ে ফেলে দিলে সমালোচনা লেখা হয় না–আর সমালোচনা না করা মানেই এই সব অসংযমী বেপরোয়া লেখককে প্রশ্রয় দেওয়া।
অতএব পড়ছি আর জ্বলছি।
সবকটা কবিতার মধ্যেই কবি তাঁর পাঠকবর্গসহ জঙ্গেলে যেতে চাইছেন। তাঁর মতে দেশটা এখন আর বাসযোগ্য নয়, এই সভ্যতার মশাল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিলে সব, এই সভ্যতার মোলায়েম হিংসা বনের হিংস্র শ্বাপদকেও হার মানিয়েছে, মানুষের মধ্যে এখন আর লোভ-লালসা দুর্নীতি-বিদ্বেষ ছাড়া আর কিছু দেখছেনই না কবি, দয়া-মায়া-ভালবাসা-মানবতার শুধু মুখোশই দেখা যাচ্ছে সর্বত্র, শাসকের বেশে শোষক ঘুরছে, ধার্মিকের বেশে অত্যাচারী ছুরি হানছে, ন্যায়ের নামাবলী পরে অন্যায়ের বিজয়যাত্রা চলেছে–অতএব এই পাপ যাদের সত্যিই অসহ্য, কবির সঙ্গে তারা যদি জঙ্গলে যাত্রা করে, তাহলে এখান থেকে অন্তত অনেক সুখে থাকবে। নমুনা দিই :
তুমি শান্তি চাও?
বুকের তলায় ডুব দিয়ে দেখো বন্ধু,
দেখো সত্যি কি চাও তুমি।
শান্তি যদি চাও,
তবে অন্য পথ নাও।
এখানে শান্তি বড় চড়া দরে বিকোয়,
এখানে প্রাচুর্যের পাপে নারায়ণ শুকোয়,
তোমার মূলধন তো কানাকড়ি!
নীতির খাপে পোরা তীক্ষ্ণ অস্ত্র নেই তোমার ঝুলিতে,
লোভের আগুন ছাই-চাপা নেই তোমার।
অহিংস উদার বুলিতে,
কথার প্রলেপে তুমি, দিন কে পারো কি রাত করতে?
আর প্রসন্ন ঢেকুর চেপে, চোখ দিয়ে পারো
সমব্যথার অশ্রু ঝরাতে?
হায় রে হায়, তোমার মূলধন যে কানাকড়ি!
তবু যদি বলো শান্তি চাই
তাহলে আমি যা বলি শোনো তাই,
চলো বন্ধু,
চলো জঙ্গলে চাই।
আমি এর পর স্নায়ু ঠাণ্ডা করার জন্যেও খানিকক্ষণ অন্যদিকে মন ফেরানো দরকার। বই রেখে খবরের কাগজ টেন নিলাম। কিন্তু এইসব অপরিণামদর্শী লেখকদের কথা ভেবে গা জ্বলছে। সরকারের ওপর এই প্রথম হয়ত একটা ব্যাপারে রাগ হল আমার –তাদের মুদ্রণ পর্যবেক্ষণ দপ্তর তো আছে একটা, এই সব বই বাজেয়াপ্ত করে না। কেন তারা? কেনই বা শান্তিপ্রিয় লোকগুলোকে এভাবে তাতিয়ে তুলতে দেয়?
খবরের কাগজে কতকগুলো ভালো ভালো খবরের ওপর চোখ বুলিয়ে মনটা একটু প্রসন্ন হল। নতুন কয়েকটা পরিকল্পনা প্রায় সমাপ্তির পথে, খাদ্য-দপ্তর খাদ্যের অনটন দূর করার দৃঢ় উদ্দীপনায় কতকগুলো ভালো ভালো ব্যবস্থায় অগ্রসর হতে চলেছেন, অন্যদিকে শাসকরা স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন–মুনাফাখোর, মজুতদার বা ভেজাল-ব্যবসায়ীদের দুর্নীতি আর তারা কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না–তাদের শুভবুদ্ধির উদ্রেক করার এবং তেমন প্রয়োজনে শাস্তি পর্যন্ত দেওয়ার রাস্তাও বার। করতে বদ্ধপরিকর তারা।
চাকর এসে খবর দিলে, নিচে একটি মেয়ে এসেছে, দেখা করতে চায়।
কে আবার মেয়ে এলো এসময়ে দেখা করতে, বুঝলাম না।
সিঁড়ির মুখে বাধা পড়ল, স্ত্রী উঠে আসছেন। আমাকে দেখে বললেন, যে লোকটা চুপি চুপি বেশি দরে, বাড়িতে মাছ দিয়ে যায় তারও আজ দেখা নেই–কী হবে?
এসব কথা কোনো দিনই ভালো লাগে না, অথচ আমারই কানে বেশি আসবে। বললাম, মাছ ছাড়াও লোকে দু দশ দিন প্রাণধারণ করতে পারে–বেশি মাংস আনিয়ে নাও, মাংস তো পাওয়া যাচ্ছে।
কিন্তু এই ফয়সালার পরেও পাশ কাটানো গেল না। তিনি আবার বললেন, কিন্তু রাঁধবে কী দিয়ে মাথামুণ্ড–দিচ্ছি দিচ্ছি করে তিন দিন ধরে তেলঅলারও তো পাত্তা নেই।
এবারে সত্যই রাগ হল, বললাম, নেই তার জন্যে মাথা খারাপ করার কী আছে? এক কালের মানুষ সব কিছু পুড়িয়ে খেত, তাদের স্বাস্থ্য, তোমার-আমার থেকে খারাপ ছিল না।
বলে ফেলেই এক ধরনের অস্বস্তি বোধ করলাম। জঙ্গলের কবির, জঙ্গলের মানুষদের সমর্থনই যেন করে ফেলা হল। নামতে নামতে আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে শুধরে নিলাম।-সেদ্ধ করেও বেশ খাওয়া চলে সব কিছু, তাতে স্বাস্থ্য বরং আরো ভালো থাকে।
নিচে অপেক্ষা করছে বছর বাইশ-চব্বিশের একটি মেয়ে। মোটামুটি সুশ্রী, ভালো। স্বাস্থ্য, একটু গম্ভীর গোছের। যে ধরনের মেয়ে দেখলে চোখে স্বভাবতই প্রীতি হয় একটু। চেনা-চেনা লাগল মুখখানা, অনেকদিন আগে কোথাও যেন দেখেছি।
মেয়েটি উঠে এসে আমাকে প্রণাম করল, কাকাবাবু ডাকল, বলল, আমাকে চিনতে। পারলেন না তো কাকাবাবু?
ওর বাবার নাম বলতেই চিনলাম, আমাদের বিনয়ের মেয়ে। স্কুল-কলেজে বিনয় আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। কোথায় একটা কেরানীগিরি করে এখন, সংসার নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে, বিশেষ দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। কিছুদিন আগে তার এই মেয়ের সম্পর্কেই কী যেন শুনেছিলাম…ঠিক মনে পড়ছে না, কী একটা কারণে মেয়েটা চাকরি ছাড়তে চায়–ওই গোছের কিছু।
মেয়েটির কথাবার্তা বেশ স্পষ্ট, সপ্রতিভ, আলগা লজ্জা-সঙ্কোচ নেই। আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করল, কোনো ভালো ভদ্র প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে চায়, আমাদের কাগজে কোনো চাকরির ব্যবস্থা হতে পারে কিনা…।
আমি অবাক একটু, কেন, তুমি তো একটা ভালো চাকরি করছিলে কোথায় শুনেছি!
জবাবে প্রায় অসঙ্কোচেই সে জানালো, ভাল চাকরিই করছিল এবং এখনো করছে। শর্টহ্যাণ্ড-জানা-গ্র্যাজুয়েট বলে চাকরি পাওয়াও সহজ হয়েছিল। তারপর স্টেনোটাইপিস্ট থেকে দেড় বছরের মধ্যেই স্টেনোগ্রাফার হয়েছে, থাকতে পারলে শিগগীরই হয়ত পি. এ-ও হয়ে যাবে। কিন্তু থাকাটাই আর সম্ভব হচ্ছে না, আত্মসম্মান বজায় রেখে সেখানে চাকরি করা কঠিন হয়ে উঠেছে। তার ঘন ঘন প্রমোশন পাওয়াটাও সকলে সুচক্ষে দেখছে না…দেখার কথাও নয়।
এইবার মনে পড়ল, ওর বাপের মুখে কী শুনেছিলাম। বাপ দুঃখ করে বলছিল, মেয়েটা যা-ও একটা ভালো চাকরি পেয়েছিল, টিকতে পারছে না। ছাড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কী যে মতিগতি হয়েছে আজকাল, ছেলে-ছোকরা ছেড়ে বাপের বয়সী অফিসাররা পর্যন্ত সোজা রাস্তায় চলে না।
যেমন বাপ তেমনি মেয়ে। বিরক্তিকর না তো কী! এই বয়সের মেয়ে পর্যন্ত একটু উদার হতে পারে না! ফ্রয়েড বা হ্যাভলক এলিস পড়া থাকলে এই সব সামান্য সহজাত বিকৃতিগুলোকে বরং একটু দরদের চোখে দেখতে পারত। দুর্নীতির মধ্যে পা না বাড়িয়েও সহজ একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তোলার বলিষ্ঠ চিন্তা এদের মাথায়ই আসে না। নীতি-নীতি করেই গেল সব, এই সামান্য কারণে একেবারে চাকরিই ছাড়তে
বিরক্তি চেপে ওকে বললাম, আমাদের কাগজের অফিসে মেয়েদের কোনো স্কোপ নেই। এও বললাম, এতেই যদি চাকরি ছাড়তে হয়, তাহলে তার উচিত কেনো মেয়ে-স্কুলে চাকরি নেওয়া।
ওপরে এসে আবার ওই জঙ্গল-ভক্ত কবির বইটাই খুলে বসলাম। প্রথমেই যে জায়গাটায় চোখ পড়ল, মনে হল চোখে যৈন পটপট করে ইনজেকশন ফোটাচ্ছে কেউ :
…তাই বলি বন্ধু, যদি সঙ্গী পাই
তবে খাঁটি সবুজ জঙ্গলে যাই।
যেখানে হিংসা খাঁটি,
আর সরলতাও।
যেখানে বাঘ ভালুক হায়না–
আপন মুখ মুখোশে ঢাকে না।
যেখানে হিংস্র চকিত হুঙ্কারে।
ভক্ষ্য হরিণের ঘাড়ে লাফায়,
রক্ষা করবে বলে তাকে
বৃথা আশ্বাসে ভোলায় না।
যেখানে শ্বাপদ-হিংসা খাঁটি
আর শশকের সরলতাও।
অরণ্যে আরো ক্ষুধা নেই একথা বলি না বন্ধু,
রিপু যেখানে আদিম আর অবিকৃত
সেখানেও বনিতার খোঁজ পড়ে অবিরত।
তবু আপন-নির্ভয়ে সেথায় বনিতারে রক্ষা করা রীতি,
আর অকপট শৌর্যে তারে জয় করা নীতি।
সেখানে ক্ষুধা খাঁটি
আর বনিতার সরলতাও।
দুইই সকলে চেনে।
যেখানে অচেনা কেউ নয়, যেমন এই সভ্যতার অরণ্যে।
তাই, আমরা যারা চেনা মুখ খুঁজে বেড়াই
তারা এসো বন্ধু,
চলো, নির্ভেজাল জঙ্গলে যাই।
জেলের বই ফেলে, সহজ দম নিতে ফেলতে সময় লাগল একটু। ভেবে আর মাথা গরম করব না, লেখার যা লিখব। পারলে জঙ্গলেই পাঠাব কবিকে। খাওয়া-দাওয়ার পর অল্প একটু ঘুমনোর অভ্যাস, তারপরে অফিস।
বাসে বসেও বইটা শেষবারের মত উল্টেপাল্টে দেখছি। আর এতে ভালো করে মন না দিয়ে মনটাকেও ঠাণ্ডা রাখতে চেষ্টা করছি। বাসে কয়েকটি ছেলেছোঁকর তরল কলরব কানে আসতে মুখ তুলতে হল। বই-খাতা নিয়ে গুটিসাতেক ছেলে কলেজে চলেছে। একজনের সামনের লেডিস সীটের একটা পাশ খালি, অন্য পাশে বছর পঁয়তিরিশেকের এক মহিলা বসে। মহিলার শৌখিন বেশবাস, চোখে পুরু কালো গগলস। রসিকতা করে ছেলেরা সকলকে শুনিয়েই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে, মহিলার পাশের ওই খালি সীটটাতে কেউ বসবে কিনা।
শেষে একটি ছেলে জিজ্ঞাসাই করে বসল, ও দিদি, বসব একটু?
না। মহিলা ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলেন, তোমরা আর একটু ভদ্র হলে বলতে হত না, আমিই বসতে বলতাম।
আর যায় কোথায়, ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়ল যেন। ছেলেরা তর্জন-গর্জন করে উঠল, এতবড় কথা! আমরা অভদ্র! মেয়েছেলে বলে যা মুখে আসে বলে পার পেয়ে যাবেন ভেবেছেন? ফর্সা জামাকাপড় পরে আর স্টাইল করে চোখে গগলস চড়ালেই মেয়েরা ভদ্র হয়ে যায়, কেমন?
বাসের দুই-একজন থামাতে চেষ্টা করল তাদের, কিন্তু তার ফল বিপরীত হল। অল্পবয়সী ছেলে সব, সত্যিই চটেছে। মারমূর্তি হয়ে তারা বলতে লাগল, কেন, কেন এই কথা বলবে আমাদের, এই সব মেয়েছেলের এত সাহস কেন? মহিলাকেই চড়াও করল আবার, আপনার মত ফ্যাশানেবল মেয়েদের খুব চিনি আমরা, বুঝলেন? আপনার মত কালো চশমা পরা মেয়েদের জানতে বাকি আছে আমাদের ভাবেন?
ক্রোধে ক্ষোভে মহিলারও আর এক মুর্তি। বলে উঠলেন, না বাবারা, এরই মধ্যে তোমরা সবই জেনে ফেলেছ, কিছুই আর জানতে বাকি নেই তোমাদের। তবে নীল চশমা কেন পরি? এই দেখো, দেখো–
বলেই একটানে চশমাটা খুলে ফেললেন তিনি। তার মুখের দিকে চেয়ে বাসের সকলেই ধাক্কা খেল একটু–ছেলেরাও চুপ কয়েক মুহূর্ত। তার এক চোখ পাথরের, এবং পাতা পড়ে না–দেখলেই অস্বস্তি হয়।
তিনি চশমাটা ফিরে পরতেই ছেলেরা আবার ক্ষেপল, আমরা এরই মধ্যে সবই জেনে ফেলেছি, কিছুই জানতে বাকি নেই–এ-কথার মানে কি? একবার অভদ্র বলেছেন, আবার আমাদের ক্যারেক্টার ধরে টানাটানি! আমরা কৈফিয়ৎ চাই, ওই চোখ দেখিয়েই আপনি আমাদের ভোলাবেন ভেবেছেন?
দাঁতে করে ঠোঁট কামড়ে বসে আছেন মহিলা। চেঁচামেচি আরো বাড়ার আগেই ছেলেদের গন্তব্যস্থান এসে গেল। আমারও। ছেলেরা শাসিয়ে গেল, তারা ছাড়বে না, এই পথে আবার দেখা হলে ভালো হাতেই মহিলাকে জবাবদিহি করতে হবে, কলেজের ছাত্রকে অপমান করে অত সহজে পার পাওয়া যায় না, ইত্যাদি।
মনে মনে আমিও ওই মহিলার ওপরেই বিরূপ হয়েছিলাম। অল্পবয়সের হাসি-খুশি ছেলে-ছোকরার দল, দেশের ভবিষ্যৎ বলতে গেলে ওরাই–কী দরকার ছিল মহিলার এভাবে ওদের বিগড়ে দেওয়া না হয়! করছিলই একটু রসিকতা, এলিস তো বলেছেন, এ-সব হল এক ধরনের সেফটি ভালভ–না সবেতেই অধৈর্য, গায়ে যেন ফোস্কা পড়েছিল।
অফিসে বসে লেখার আগে আর একবার সেই জঙ্গলের কাব্য খুলেছি। পড়বি তো-পড় এমন জায়গাই চোখে পড়ল যে হাতের কলম আছড়ে মারতে ইচ্ছে করে :
তবু আশা বন্ধু? এখনো আশা?
এখনো কিছু দেখতে বাকি!
এখনো ভাবো, আরো একটু থাকি!
এখনো আশা, নতুন কণ্ঠে শুনবে ভাষা?
শোনো বন্ধু, অরণ্যে দাউদাউ দাবাগ্নি জ্বলে
সেই আগুনে বস্তু পোড়ে, অরণ্যের প্রাণ পোড়ে না।
তোমাদের এই সভ্যতার আলোর তলায় মশাল জ্বলে,
এই আগুনে মানবতা পোড়ে, বস্তু পোড়ে না।
নতুন অরণ্য জাগে।
ঋতুস্নাতা ধরণীর অনুরাগে।
কিন্তু তোমার নগরে নতুন মানুষ কারা?
মানবতা-পোড়া বস্তুর, সন্তান যারা?
অনেক তো দেখেছ বন্ধু,
অনেক জেনেছ,
শক্তির দম্ভ আর লোভীর হীনতা
পণ্ডিতের দর্প আর জ্ঞানীর মূঢ়তা
প্রাচীনের গর্ব আর নবীনের ক্লীবতা
এরা কি শোনাবে বলো নতুন দিনের বারতা?
অনেক দেখেছ বন্ধু, অনেক জেনেছ।
তবু আমিও তোমারই মত কিছু আশা চাই,
তাই ডাকি বন্ধু, চলো,
এবারে অকৃপণ উদাত্ত গম্ভীর জঙ্গলে যাই।
বই ফেলে দিয়ে কলম হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ভাবলাম, কি লেখা যায়, কেমন করে উপযুক্ত ঘা দেওয়া যায়। ভাবতে ভাবতে শুভবুদ্ধিই মনে জাগল। সব থেকে ভালো অবজ্ঞা করে যাওয়া, এর অস্তিত্বই অস্বীকার করা। এ ধরনের অবাঞ্ছিত বইয়ের বিরুদ্ধে জোরালো রকমের হাঁকডাক করলেও অপরিণত বয়সের ছেলেমেয়েদের কৌতূহল বাড়বে। একবার পড়ে দেখার জন্যও বইখানা হয়ত বা তাদের কেনার আগ্রহ হবে। তাদের প্রতি গুরুদায়িত্বের কথা ভেবেই কলম বন্ধ করলাম।
না, সমালোচনা লিখব না।
তমোঘ্ন
এই পাহাড়ী মরুরাজ্যে হৃদয়ের চাষ নেই। পাহাড়গুলো সব অতিকায় হাড়গোড় বার-করা পাথরের স্তূপ। বড় বড় গাছগুলোর প্রায় বারো মাসই কঙ্কাল-মূর্তি। সন্ধ্যের আগে পর্যন্ত মাথার ওপর সূর্য জ্বলে। শুকনো হাঁ-করা মাটির রং বাদামী। দূরে মরুভূমি।
এখানে সব থেকে দুর্লভ মানুষের হৃদয় নামে বস্তু।
মানুষগুলো খেতে না পাক, নেশা করে। এই বস্তুর জন্য ওরা প্রাণ দিতে পারে, প্রাণ নিতে পারে।
কিন্তু পুরুষদের সব থেকে বড় নেশা ভাটিখানা বা ঘরের তৈরি রক্তে-আগুন ধরানো পচাই নয়। তার থেকেও অনেক বড় নেশা আছে।
প্রতিশোধের নেশা।
চকচকে ছুরির ফলা বুকে আমূল বিদ্ধ হলে ফিনকি দিয়ে তাজা রক্তের ফোয়ারা ছোটে যখন, ওদের সে উল্লাস দেখলে এই সভ্য দুনিয়াটাকে বহু শতাব্দী পিছনের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া চলে।
চিমনলালের ছেলে রোশনলাল দীর্ঘ তিন বছরে এই একটি নেশার সাধনায় স্তব্ধ হয়ে আছে।
প্রতিশোধ!
দুটি মৃত্যু চাই তার। এমন মৃত্যু যা কখনো কেউ কল্পনা করতে পারে না। একটা মৃত্যু অন্তত সেই রকম হবে। একটা একটা করে চোখ উপড়ে নেবে, একটু একটু করে গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নেবে–আরও অনেক পরে আসবে মৃত্যু।
আর একটা মৃত্যু কেমন হবে, রোশনলাল এখনো স্থির করে উঠতে পারে নি। সেও চমকপ্রদ যে হবে সন্দেহ নেই।
প্রতিশোধের এই লগ্নকাল উপস্থিত। রোশনলাল হদিস পেয়েছে ওদের। দলের একজন দূরে চলে গেছল, সে ফিরে এসে হদিস দিয়েছে। এখান থেকে দশ মাইল দূরে এক ছন্নছাড়া গাঁয়ে বাসা বেঁধেছে ওরা।
খবরটা শোনামাত্র শিরায় শিরায় কী কাণ্ড ঘটে গেছে তা শুধু রোশনলালই জানে। আর অনুমান করতে পারে তার অতি বিশ্বস্ত প্রধান চারজন সঙ্গী।
দুশ মাইল আর কতদূর?
রোশনলাল বাপের মন্ত্রে দীক্ষিত। প্রতিশোধ কী করে নিতে হয় সেটা সে বারো বছর বয়সে স্বচক্ষে দেখেছে।
অবশ্য সেও সেদিন বাপকে ঘৃণা করত আর ভয় করত। পছন্দ বরং তখন মাকেই করত। বেশ সুশ্রী ছিল তার মা।
সেই রাতটা মনে আছে রোশনলালের।
তারা থাকত তখন পশ্চিমঘাটের এক পাদার আশ্রয়ে। সেখানকার কর্মচারী ছিল তার দুর্দান্ত বাবা। পাদ্রী জোসেফের ঘরে থাকত তার আট বছরের একটা ফুটফুটে মেয়ে। হীরা-হীরা জোশেফ। সকলে বলে কুড়নো মেয়ে, অনেকে আড়ালে বলে জোশেফেরই মেয়ে। ওই মেয়েটাকে মা ভারী ভালবাসত।
কদিন ধরে মায়ের মুখখানা খুব শুকনো দেখছিল রোশনাল। নিশ্চয় বাবার ভয়ে। বাবাকে যমের মত ভয় করত মা।
…সেই একটা রাত। ঘরে মা দাঁড়িয়েছিল। সেখানে রোশনলাল ছিল আর হীরা ছিল। দেয়ালে টাঙানো মস্ত একটা ছবি ছিল। ছবিতে খোলাচুল লালচে রঙের একটা মেমসাহেব, তার বুকে মাখমের ডেলার মত একটা ছেলে। মা সেই দিকে চেয়ে ছিল। রোশনলাল জিজ্ঞাসা করেছিল, ওরা কারা?
বিড়বিড় করে মা কী যে জবাব দিয়েছিল কিছুই বোঝেনি। বলেছিল, বিশ্বমায়ের কোলে মানবপুত্র বিশ্বশিশু।
না বুঝলেও রোশনলালের একটা দৃশ্য ভাবতে বেশ ভালো লেগেছিল। সেও একদিন ওই ছবির বাচ্চাটার মতো ছোট ছিল, আর তার মা হয়ত তখন অমনি তাকে বুকে করে দাঁড়িয়ে থাকত।
বাবা হঠাৎ ঘরে ঢুকে মা কে ডাকতে এসেছিল। মা চমকে উঠেছিল। বলেছিল, যাবে না।
সেই রাতে বাবার হ্যাঁচকা টানে ঘুম ভেঙে গেছল। পাশে চোখ যেতেই রোশনলাল ভয়ে নীল হয়ে গেছল। মায়ের দেহ রক্তে ভাসছে।
বাবার সেই মুখের দিকে চেয়ে অস্ফুট আর্তনাদও করতে পারে নি রোশনলাল। বাবা তাকে তুলে নিয়ে যে-ঘরে ঢুকেছে সেটা পাদ্রী জোসেফের ঘর। সেও মৃত। রক্তে ভাসছে। অদূরের শয্যায় হীরা ঘুমিয়ে। বাবা তাকে তুলে নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এসেছে।
তিন-চারটে রাতের অন্ধকারে অন্ধকারে কোথায় কতদূরে চলে এসেছিল জানে না।
যেখানে এসেছিল, সেখানে চেনা-মুখ দেখেছে জন-কতক। বাবার বন্ধু। মাঝে মাঝে পাদ্রী জোসেফের ওখানে এসে বাবার সঙ্গে দেখা করত তারা।
একেবারে অবুঝ নয় রোশনলাল তখন। মা আর পাদ্রী জোসেফের মৃত্যুর কারণ অনুমান করতে পারে। আর একটু বড় হবার পরে স্পষ্টই বুঝেছে।
রোশনলাল ভেবেছিল হীরাকেও বাবা মেরেই ফেলবে। নিজের মেয়ে হোক না হোক, হীরাকে খুব ভালবাসত পাদ্রী জোসেফ, আর তার মা তো ভালবাসতই–অতএব বাবার রাগ ওর ওপরেও পড়বেই ধরে নিয়েছিল।
কিন্তু কিছুকাল যেতে দেখা গেল, বাবার টান তার থেকেও হীরার ওপর বেশি। হীরা ওর নামে বাবার কাছে নালিশ করলে বাবা ওকে তুলোধুনো করে, কিন্তু হীরার নামে নালিশ করলে কিছুই বলে না।
আট বছর কেটে গেছে। রোশনলালের বয়েস কুড়ি, হীরার সোল।
বাবার পক্ষপাতিত্বের দরুন হীরাকে অনেকবার খুন করতে সাধ গেছে। কিন্তু এখন আর তা হয় না। হীরাকে দেখলে রক্তে এখন অন্য রকমের নাচন-মাতন শুরু হয়। মাথায় গ্রাসের আগুন জ্বলে। হীরা সেটা বুঝতে পারে। একলা থাকলে বেশি কাছে ঘেঁষে না।
মাথা খাটিয়ে কৌশলে এক রাতে ওকে পাহাড়ের আড়ালে অন্ধকারে টেনে নিয়ে গেছল। রক্তে সবে নেশা লেগেছিল। সরল দুটো বাহুর নিষ্পেষণে হীরা অপুট আর্তনাদ করে উঠেছিল। আর হিংস্র অধরদংশনে রোশনলাল তাকে শাসাচ্ছিল, টু-শব্দ করলে একেবারে খুন করে পাথরের তলায় পুঁতে রেখে চলে যাব!
কিন্তু পরের মূহুর্তে নিজেরই রক্ত জল। আচমকা আঘাতে চোখের সামনে মৃত্যুর অন্ধকার। সেই অন্ধকার কুঁড়ে তার বাবা দাঁড়িয়ে।
রোশনলালের ধারণা, এই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে সূরযপ্রসাদ। সে-ই হীরার পিছনে ছায়ার মতো ঘোরে সর্বদা। দুটিতে খুব ভাব, সে-ই কোথাও থেকে দেখে থাকবে। বাবাকে বলে দিয়ে থাকবে।
তার খাতায় সূরযপ্রসাদের পরমায়ুতে সেদিনই ঢ্যারা পড়ে গেছল।
দলে অনেক ছেলেছোকরা এসেছে এখন। সকলের থেকে অকর্মণ্য ওই চাষীর ছেলে সূরপ্রসাদ। চিমনলাল দলের সর্দার, রোশনলাল তার ডান হাত। সকলের ধারণা, কালে-দিনে বাপের থেকে দ্বিগুণ দুর্ধর্ষ হবে রোশনলাল, কিন্তু এই ছেলেকেও বাপ সেদিন ক্ষমা করেনি। তিনদিন তিনরাত ঘরে তালা দিয়ে ফেলে রেখেছিল। খেতেও দেয়নি। খুপরি জানলা দিয়ে ওই হীরা চুপি চুপি কিছু খাবার ফেলে না দিলে প্রাণে বাঁচত না।
তারপর বাবা তাকে বলেছিল, সময় হলে হীরার সঙ্গে আমিই তোর বিয়ে দেব, কিন্তু তার আগে ওর গায়ে হাত দিলে কেটে দুখানা করে ফেলব।
গায়ে আর হাত দেয়নি। কিন্তু কবে যে বাবার সময় হবে তা ভেবে পায়নি।
আরো দীর্ঘ চারটে বছর কেটেছে। রোশনলালের চব্বিশ আর হীরার কুড়ি।
চিমনলাল বলেছিল, এ বছরটা কাটলে ছেলের বিয়ে দেবে। রোশনলালের মনে হয়েছিল, মায়ের মৃত্যুর বারো বছর পার হওয়ার অপেক্ষায় আছে তার বাবা। অনেক ব্যাপারে বারো বছরের সংস্কার মানে তাদের সমাজের মানুষ।
কিন্তু বিয়ে দেওয়ার সময় বাবার আর হল না। ছোটখাট রাহাজানি করতে গেছল কোথায়। পাঁজরে গুলি খেয়ে ফিরল। পরদিন শেষ।
রাতারাতি চরিত্র বদলে গেল রোশনলালের। সে দলপতি। তিনদিনের মধ্যে বাপের মৃত্যুর মর্মান্তিক প্রতিশোধ নিল। তারপর দলটাকে নতুন উদ্দীপনায় তাজা করে তুলতে লাগল সে।
হীরাকে বিয়ে এবছরের পরেই করবে। বাপের ইচ্ছের অসম্মান করবে না।
খবর পেল, সুর্যপ্রসাদের আর দলে থাকার ইচ্ছে নেই, দেশে ভদ্র জীবনযাপনের মতলবে আছে সে।
রোশনলালের আপত্তি ছিল না। বাপের আমলেও কোনো কাজে লাগেনি, এখনো ওর মত অকর্মণ্য আর কেউ নয়। কিন্তু অনুমতি পেয়েও কেন যে গেল না, তখন বোঝেনি।
কদিন ধরে একটা কানাঘুষা শুনছিল। হীরার সঙ্গে সূরযপ্রসাদের ইদানীং ভাব সাব একটু বেশিই দেখছে সকলে। আত্মপ্রত্যয়ে ভরপুর রোশনলাল এসব তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। আর আসলে মেয়েটাই বজ্জাত, তাও জানে। যখন-তখন হীরাই ওকে ডাকে। মেয়েদের মন জুগিয়ে চলার মতো মরদ ওর দলে এক সুর্যপ্রসাদ ছাড়া আর কে আছে!
তবু মেজাজ বিগড়েছিল একদিন। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে একটা নিরিবিলি জায়গায় বসে ওদের দুজনকে হাসিমসকরা করতে দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। তার হাতের একটা চড় খেয়ে তিন হাত দূরে ছিটকে পড়েছিল সূরযপ্রসাদ। তারপর। উঠে খরগোশের মত পালিয়েছিল।
হীরা ফুঁসে উঠেছিল, ওকে মারলে কেন? জবাবে চুলের মুঠি ধরে তার মাথাটাও পাথরে বারকয়েক ঠুকে দিয়েছিল রোশনলাল।
শিকারে বেরিয়েছিল, দুদিন বাদে ফিরে দেখে ঘরে হীরা নেই। তারপর দেখা গেল সুর্যপ্রসাদও নিখোঁজ।
এত সাহস দুনিয়ায় কারো হতে পারে রোশনলাল কল্পনা করতে পারে না।
তারপর থেকে রোশনলাল ক্ষিপ্ত, উন্মাদ। অনেকবার রক্তরাঙা হয়েছে তার এই দুটো হাত।
সমস্ত অঞ্চল আঁতিপাতি করে খুঁজেছে। সন্দেহবশে কোথা থেকে কোথায় ছুটে গেছে ঠিক নেই। সভ্য দুনিয়া তাকে পেলেই ধরে ফাঁসিকাঠে ঝোলবে জানে, তবু গেছে।
কিন্তু ওরা যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে। কবছরের মধ্যে সন্ধান মেলেনি। এই চার বছরের মাথায় মিলেছে।
রাতের অন্ধকারে চারজন যোগ্য সঙ্গী নিয়ে একদিন রোশনলাল পা ফেলেছে এই দুশ মাইল দূরের এলাকায়। তার চোখে সাদা আগুন, চোয়াল দুটো লোহার মত শক্ত
রাতেই খবরাখবর নেওয়া শেষ।
পরদিন সকালে পুরুষেরা সব চলে যাবে চার মাইল দূরের হাটে। সুরপ্রসাদও যাবেই। রোশনলালের সঙ্গীরা যেমন করে থোক সেখান থেকে তাকে গায়েব করবে। নিতান্ত না পারে যদি, সেখানে নৃশংসভাবে হত্যা করবে তাকে।
…আর রোশনলাল একা যাবে হীরার কাছে। একশ দেড়শ গজ দূরে দূরে ছাড়া ছাড়া বসতি। হীরার ঘরের শগজ ছাড়িয়ে কয়েকটা বুড়োবুড়ির ঘর–তাও সে-ঘরে বুড়োরা থাকবে না তখন। তারা হাটে যাবে।
পটভূমি প্রস্তুত।
সমস্ত রাত ঘুম হল না রোশনলালের। পচায়ের স্রোত জঠরে ঢেলে মাথার আগুন ঠাণ্ডা করা গেল না।
কী করবে সে? প্রথমেই হত্যা করবে?
না। তার বিশ বছর বয়স থেকে ভিতরের যে পশুটা বুভুক্ষু, প্রথমে তাকে ছেড়ে দেবে। হীরার তখন আশা হবে। তার নারীদেহের লোভে ডুবিয়ে মানুষটাকে বশীভূত করা গেল ভাববে। আতঙ্কে ত্রাসে বোবা হয়ে যাবে পরক্ষণে। চোখ বোজারও অবকাশ পাবে না, ধারালো ছোরাটা তার নরম বুকের উষ্ণ তাজা রক্তে স্নান করে উঠবে।
.
পরদিন।
প্রতীক্ষিত সময় এলো।
সঙ্গী চারজন নির্দেশমত হাটের দিকে চলে গেল।
রোশনলালও তার পথে পা বাড়ালো।
দূরে দাঁড়িয়ে হীরা আর সূরযপ্রসাদের ঘরটা ভালো করে দেখল একবার। তারপর আস্তে আস্তে কাছে এগিয়ে এলো।
দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। পলকা দরজা, অনায়াসে ধাক্কা দিয়ে ভেঙে ঢুকতে পারে। কিন্তু তার দরকার হবে না বোধহয়।
দরজায় বার-কয়েক মৃদু আঘাত করতে ওদিক থেকে সাড়া মিলল।
কয়েক পা পিছিয়ে এসে রোশনলাল প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল।
দরজা খুলে হীরা বেরিয়ে এলো।
কিন্তু নিমেষের মধ্যে চোখেমুখে সমগ্র সত্তায় এ কিসের আচমকা ঝাঁপটা খেল রোশনলাল? সবকিছু ধাঁধিয়ে দেবার মতো, অন্ধ করে দেবার মত আলোর ঝাঁপটা!
পাদ্রী জোসেফের ঘরের দেয়ালের ছবির মতো এক অনির্বচনীয় রমণী-মূর্তি, কোলে তার ফুটফুটে ছেলে একটা। মা বলছে, বিশ্বমায়ের কোলে মানবপুত্র বিশ্বশিশু। .যা দেখে রোশনলালের ভাবতে ভালো লাগত, সেও একদিন ওই ছবির বাচ্চাটার মতো ছোট ছিল, আর তার মা হয়ত তখন অমনি তাকে বুকে করে দাঁড়িয়ে থাকত।
না, ছবি নয়। সামনে হীরা দাঁড়িয়ে। বুকে তার দু-বছরের ফুটফুটে ছেলে একটা।
তাকে দেখে হীরা চমকে উঠেছিল কিনা, ত্রাসে বিবর্ণ হয়েছিল কিনা–ওই আলোর ঝাঁপটা খেয়ে রোশনলাল কিছুই লক্ষ্য করেনি। স্থির দাঁড়িয়ে হীরা এখন তাকেই দেখছে। তার বিভ্রম অনুভব করছে।
জোসেফের ঘরের ছবির রমণী কখনো কথা বলেনি। এই রমণী বলল।–বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে এসো। সূরযপ্রসাদ হাটে গেছে।
স্থান-কাল ভুলে ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিল রোশনলাল, দেখছিল। মিষ্টি মৃদু কথা কটা কানে যাওয়া মাত্র বিষম চমকে উঠল। নিজের মাথার উপর উদ্যত খড়গ দেখলেও কেউ এমন চমকায় না বোধহয়।
চকিতে আর একবার শুধু সামনের জীবন্ত চিত্রটা দেখে নিল। পরক্ষণে উধ্বশ্বাসে ছুটল হাটের পথ ধরে।
একটু দেরি হয়ে গেলে চরম সর্বনাশ আর ঠেকানো যাবে না বুঝি।
পরনে ঢাকাই শাড়ি
স্বপ্নের গাছে বাস্তবের ফল সত্যিই ধরে?
বিজন ঘোষ চৌরঙ্গী এলাকায় এসেছিল একটা ওষুধের খোঁজে। কদিন আসবে আসবে করে সময় করে উঠতে পারেনি। তার কর্মক্ষেত্র সুদূর দক্ষিণে। থাকেও সেদিকেই। কিন্তু ওষুধটা আর না কিনেলই নয়। সমস্ত দক্ষিণ কলকাতা চষে পায় নি! আপিস থেকে একটু আগে বেরিয়ে এসেছে মধ্যস্থলে।
ওষুধটা পাওয়া গেল। ফেরার বাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল।
তখনি যোগাযোগ।
একটা কাগজের প্যাকেট বুকে করে ফুটপাথ ছেড়ে রাস্তা পার হবার তোড়জোড় করছিল প্রমীতা গুপ্ত। পরিচিত ফ্যালফেলে চাউনির চেনা-মুখ দেখে দাঁড়িয়ে গেল। বিস্ময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিড়ম্বনার চকিত কারুকার্য একটু। পলকের দ্বিধা। তারপর মিষ্টি আর ভারী অবাক মুখ করেই প্রমীতা কাছে এগিয়ে এলো।–তুমি! কী আশ্চর্য!
বিজন ঘোষের মুখে লাজুক হাসি। কাছে এসে দাঁড়ানোর পর অবাধ্য চোখ দুটো প্রমীতার মুখের ওপর থেকে নড়তে চাইছে না। পলকের দেখার মধ্যে চৌদ্দ বছরের অদেখার একটা দুস্তর সমুদ্র পাড়ি দেবার বাসনা।
–দেখছ কী এমন করে, চিনতে পারছ তো?
বিজন ঘোষের হাসি-হাসি মুখ, কিন্তু চোখের তারা দুটো বড় বেশি স্থির তার মুখের পর। মাথা নাড়ল, অর্থাৎ চিনতে অনায়াসেই পেরেছে। বলল, তুমি রাস্তা পার হতে চেষ্টা করছিলে দেখছিলাম।
-বলো কি, দেখেও ডাকোনি?..নাকি ডাকতে চাওনি?
–মনে মনে ডাকছিলাম, ভরসা করে গলার আশ্রয় নিতে পারিনি।
প্রমীতা হঠাৎ হেসে উঠল। ফর্সা মুখখানা খুশি-খুশি দেখালো। পা থেকে মাথা পর্যন্ত একনজর দেখল তাকে। পরনের ধুতিটা পরিষ্কার, গায়ের মূগা-রঙা পাঞ্জাবিটা আধময়লা–কিন্তু একটু মোটা হয়েছে, আর মুখখানাও আগের থেকে ঢলঢলে হয়েছে। বলল, তুমি একেবারে আগের মতই আছ দেখছি, কত বছর পরে দেখা বলো তো!
–চৌদ্দ বছর। রামচন্দ্রের বনবাসের কাল।
-এত হিসেবও রেখেছ! উৎফুল্ল মুখে প্রমীতা জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু তুমি কলকাতায় কবে থেকে? আমি তো শুনেছিলাম পাকাপাকি পশ্চিমবাসী হয়ে গেছ?
বছরখানেক হল কলকাতাবাসী হয়েছি, বিহারী আপিসের কলকাতায়। শাখা-বিস্তার হয়েছে। দড়ি।
প্রমীতা সকৌতুকে তাকালো তার দিকে।–এক বছরের মধ্যে মনে পড়ল না, আমাদের বাড়ির রাস্তাটা ভুলে গেছ বুঝি?
বিজন হাসতে লাগল। হাসিটা মিষ্টি লাগছে প্রমীতার, কিন্তু মুখের ওপর ওই চাউনিটা অস্বস্তিকর। জবাব দিল, ভুলিনি…রাবরই সাহসের অভাব তো! তাছাড়া ভেবেছিলাম তুমিও ঘর বদলেছ।…কিন্তু কী ব্যাপার, সীমন্তে দাগ দেখছি না যে?
নিমেষে মুখের রঙবদল হল যেন একট, তারপর হাসি-মাখা দুচোখ তার চোখের ওপর তুলল প্রমীতা। লোকটার কথাবার্তার ধরনও যেন আগের থেকে তাজা হয়েছে মনে হল। বলল, দাগ ফেলার মত লোক আর এলোই না, তার কী করা যাবে? মুখ আবারও রাঙালো একটু, তাড়াতাড়ি বলল, চলো কোনো ভালো জায়গায় বসে একটু চা বা কফি খাওয়া যাক, তোমার তা নেই তো কিছু?
খুশিমুখে বিজন পকেটে হাত ঢোকালে, দাঁড়াও, পকেটে রসদ কী আছে। দেখি
দেখতে হবে না, এসো।
স্মিতমুখ দুজনেরই। পাশাপাশি কোনো রেস্তরাঁর উদ্দেশে এগোলো তারা।
.
আপিসের হিসেব রাখার কাজ করে বিজন ঘোষ। জীবনের হিসেবও ভোলেনি। আর দেখা না হলেও প্রমীতা গুপ্তর খবর রাখে না এমন নয়। কোন এক বে-সরকারী কলেজে প্রোফেসারি করে এই খবর রাখে, সমন্তে এখনো দাগ পড়েনি এবং পড়ার সম্ভাবনাও বিশেষ নেই–এ-খবরও রাখে। আর চৌরঙ্গিপাড়া থেকে বিলিতি বই কিনে আর পড়ে অবসর সময় কাটায়, হাতের প্যাকেট দেখে অনুমানে সে-খবরটা আজ পেল।
…বিজনের উনচল্লিশ চলছে, প্রমতার বয়েস তাহলে এখন ছত্তিরিশ হবে। দেখায়ও তার থেকে কম নয়, ফর্সা মুখ আগের থেকে আরো ফ্যাকাশে হয়েছে।
.
আঠারো বছর বয়সে পনের বছরের মেয়ে প্রমীতার প্রেমে পড়েছিল বিজন ঘোষ। ভীরু প্রেম। বাইরের প্রকাশ আরো উক্ত। কিন্তু ভিতরে প্রেমানলের স্রোত।
তার মামাতো বোন শেফালীর সহপাঠিনী ছিল। মামারবাড়িতে থেকেই পড়াশুনা করত বিজন ঘোষ। সেই সূত্রেই বাড়িতে যাতায়াত আর পরিচয়। শেফালী খানিকটা করুণার চোখে দেখত ভালোমানুষ পিসতুতো দলটিকে। প্রমীতার চোখও তার থেকে ওপরে ওঠেনি। গরীব ঘরের মেয়ে শেফালীর সতেরোয় বিয়ে হয়ে গেছে। গল্পের বই যোগান দিয়ে, সিনেমার টিকেট কেটে দিয়ে, আরো অনেক-রকম সরল কৌশলে প্রমীতার সঙ্গে যোগাযোগটা অন্তরঙ্গ করে তুলেছিল বিজন ঘোষ। অন্তরঙ্গতা শুধু তার। দিক থেকেই, প্রমীতার দিক থেকে সেটা প্রীতি-দাক্ষিণ্যের বেশি নয়।
ফেল করার মত ছাত্র ছিল না বিজন ঘোষ। কিন্তু রয়েসয়ে এক বছর পর এক বছর ফেল করে করে এম-এ ক্লাসে উঠে প্রমীতার সহপাঠী হবার সৌভাগা অর্জন করেছিল সে। আর খুশিমুখে কৌশলে এই ফেল করার উদ্দেশ্যটা প্রমীতাকে জানিয়েছিল।
বিস্ময় ছাপিয়ে প্রমীতার ভ্রকুটি বেশি ঘন হয়ে উঠেছিল। তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে! কেন?
এই কেনর জবাব প্রমীতা যদি নিজের থেকে বুঝে না নেয়, বিজন ঘোষ কী বলতে পারে!
সিক্সথ ইয়ারে উঠে প্রমীতার বিরক্তিটা প্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সর্বদা যদি একটা লোক ছায়ার মত লেগে থাকে, কাহাতক ভালো লাগে! বন্ধুরা মুখ টিপে হাসে, সীতা দেবীর ভক্ত হনুমান বলে ওকে নিয়ে আড়ালে ঠাট্টা-তামাশাও করে– প্রমীতা তাকে বলেছেও সে-কথা। কিন্তু বলার উদ্দেশ্য সফল হত বোঝারও চেষ্টা যদি থাকত।
ওই সময়েই কোথা থেকে ভালো একটা বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল তার, বিজন। খবরটা জানতে পারার পর এই দীর্ঘ ব্যাপারটার ছেদ।
আমতা-আমতা করে শুকনো মুখে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল সে। তখনি নয়। অবশ্য, এম-এ পাশ করার পর, আর ভালো চাকরি জুটিয়ে যোগ্যতা অর্জনের পর। সে শুধু ভবিষ্যতের আশ্বাসটুকু চায়।
মুখের দিকে চেয়ে কটু কথা বলা দূরে থাক, আশ্বাসটুকু ধূলিসাৎ করতেও কষ্ট হয়েছিল প্রমীতার। আবার এরকম সম্ভাবনার কথা ভাবতেও রাগ হচ্ছিল। খানিক চুপ করে থেকে জবাব দিয়েছিল, মাকে গিয়ে বলো, এ-সব আমি কিছু জানি না।
প্রমীতা সেদিনই মাকে একটু আভাস দিয়ে রেখেছিল, ভদ্রভাবে বেশ স্পষ্ট করেই। যেন প্রস্তাবটা নাকচ করা হয়।
প্রমীতার মা ওই সাদামাটা নিষ্প্রভ ছেলের দুঃসাহসিক অভিলাষের কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। প্রস্তাবটা আর তার কাছে ভালো করে উত্থাপনও করতে পারেনি বিজন ঘোষ। তার আগেই বেশ স্পষ্ট অনুশাসনের সুরে আর এ-বড়ি আসতে বা প্রমীতার ছায়া মাড়াতেও নিষেধ করে দিয়েছিলেন তিনি।
কৃতী স্বামী আর চার-চারটে কৃতী ছেলের পর ওই একটিমাত্র মেয়ে তাঁর। রাগ হবারই কথা।
এর পরদিন থেকে প্রমীতা আর তাকে দেখেনি। য়ুনিভার্সিটিতেও আসে নি বিজন ঘোষ, অর্থাৎ এম-এ পড়া সেখানেই খতম হয়েছে। পরে কার কাছে শুনেছে, এ দেশ ছেড়েই চলে গেছে সে, বিহারে না কোথায় চাকরি নিয়েছে।
লোকটা দুঃখ পেয়ে গেল বলে প্রমীতার অবশ্য কষ্টই হয়েছিল, কিন্তু কী আর করতে পারে সে!
প্রমীতার জীবনেও অনেক জল ঘোলা হয়েছে এর পর। জামাই বাছতে বাছতে হঠাৎ একদিন চোখ বুজেছেন তার মা। তারপর প্রমীতা নিজেও অনেক সম্ভাব্য পাত্র বাতিল করেছে, আবার কেউ কেউ তাকেও বাতিল করেছে। এমনি এক বাতিলের ব্যাপার নিয়ে রীতিমত অপমানকর ব্যাপার ঘটে যায় একটা। বাবাকে আর তার বিয়ে নিয়ে মাথা ঘামাতে নিষেধ করে প্রমীতা কলেজে চাকরি নিয়েছে। বয়েস এখন। ছত্তিরিশ…চাকরিই করে যাচ্ছে। ক্লান্তিকর অবকাশ কাটানোর জন্যে মাঝে মাঝে এ পাড়ায় এসে বিলিতি বই কেনে।
জীবনের এই সীমান্তে এসে বিজন ঘোষের সঙ্গে দেখা।
.
একটা ক্যাবিনে মুখোমুখি বসেছে দুজনে। বয় এসে দাঁড়িয়েছে। প্রমীতা জিজ্ঞাসা করল, চা না কফি?
-কফি হোক। অনেকদিন ও বস্তু জিভে ঠেকাইনি।
এই সরলতা কানে বেশ ভালো লাগল প্রমীতার। হেসে বলল, আর কি?
-আর কিছু না।
বয় কফির অর্ডার নিয়ে গেল আর দিয়ে গেল। কফি তৈরি করে পেয়ালা এগিয়ে। দিল প্রমীতা, নিজেরটাও টেনে নিল। সহজ অন্তরঙ্গতার সুরেই জিজ্ঞাসা করল, তারপর, এখানে আছ কোথায়?
–সেই দক্ষিণে।
–দক্ষিণে কোথায়?
–কেন, যাবে?
আবারও মুখের উপর চোখ দুটো বড় বেশি স্থির মনে হল প্রমীতার। হেসেই জিজ্ঞাসা করল, কেন, গেলে কারো আপত্তির কারণ হবে?
বিজন হাসছে মৃদু মৃদু–তা হবে না অবশ্য। বাড়ি পনেরোর দুই, ভবেন হালদার লেন, চারু মার্কেটের কাছে।
–ঠিক যাব একদিন দেখো, ছুটির দিনে থাকো তো?
বিজন মাথা নাড়ল, থাকে। ওষুধের বোতলটার দিকে চোখ পড়তে প্রমীতা জিজ্ঞাসা করল, ওষুধ মনে হচ্ছে, কার?
–মেজ মেয়ের। ও-পাড়ায় পেলাম না।
ঠিক সেই মুহূর্তে প্রমীতার মুখখানা নিষ্প্রভ দেখালো একটু, গলার স্বরও বদলালো যেন। কিন্তু মুহূর্তের ব্যতিক্রম মাত্র, তারপরে হেসেই বলল, সংসারচিত্রের প্রথমেই মেয়ের অসুখের খবর দিলে! কী হয়েছে?
-পেটে চিনচিনে ব্যথা, প্রায়ই ভুগছে, আজও ওষুধটা না নিলে খণ্ড-প্রলয়ের সম্ভাবনা ছিল।
পরিতুষ্ট মন্তব্যের মত শোনালো প্রমীতার কানে। হেসেই জিজ্ঞাসা করল, ছেলেপুলে কী তোমার?
–দুই মেয়ে, এক ছেলে।
কার কত বয়েস? সত্যিই এই লোকটার সম্পর্কে জানার কৌতূহল প্রমীতার।
–বড় মেয়ে এগারো, মেজোটা সাড়ে আট, ছেলে সারে ছয়।
–বেশ। এবার বউ কেমন শুনি?
–বিয়ের পর একবছর পর্যন্ত বউ ছিল, এখন তিনি কর্তা–আমার পোজিশন ছেলে-মেয়েদের থেকে খুব বেশি ওপরে নয়। নিজেও কিছু উপার্জন করে বলে আমাকেও প্রায় অকর্মণ্য পোষ্য ভাবে।
–চাকরিও করে তাহলে! লেখা-পড়া জানা বলো..কী চাকরি?
-মাস্টারী। তবে তোমার মত বড়দরের নয়, ছোটদরের। দিনের বেলায় স্কুলের। মেয়েদের ওপর, রাত্রিতে আমাদের ওপর।
প্রমীতা লক্ষ্য করছে, মুখখানা আগের থেকে সত্যিই অনেক ঢলঢলে হয়েছে, আর প্রকারান্তরে যতই বউয়ের নিন্দার আভাস ফোঁটাতে চেষ্টা করুক, কথাবার্তায় আসলে বেশ একটা সহজ পরিতৃপ্তির আমেজ রয়েছে।
হেসে ছদ্ম ভ্রূকুটি করল প্রমীতা, বিচ্ছিরি কথাবার্তা হয়েছে তো তোমার! দাঁড়াও, বাড়ি গিয়ে যা-যা বলেছ, বউকে বলে দেব সব!
-বোলো। বিশ্বাস করলে আমাকে ধোলাই করতে নিশ্চয় ছাড়বে না, কিন্তু তোমার। মত এমন পরিচিত একজনও আছে আমার, চাক্ষুষ সে-প্রমাণ পেলে মনে মনে একটু সম্মানও অন্তত নিশ্চয় করবে–আমার কপালে এ বস্তুটি দিনকে দিন দুর্লভ হয়ে উঠছে।
চারুমার্কেট ছড়িয়ে, ট্রামডিপো ছাড়িয়ে, আরো আধমাইল পথ পায়ে হেঁটে অন্ধকার গলির ভিতর দিয়ে ঠাওর করে এগিয়ে এসে জীর্ণ বদ্ধ দরজার তালা খুলল বিজন ঘোষ। নিঃশব্দ হাসিটা সমস্ত মুখে ছড়িয়ে আছে।
বগলের ওষুধটা নিজেরই, পেটের চিনচিনে ব্যথাটাও নিজেরই। কিন্তু ওষুধটা না কিনলেও হত, ব্যথাটা বোধ হয় সেরেই গেল। প্রমীতা কোন দিনও আর তার ঘরে আসবে না। এলেও চারুমার্কেটের সামনে পনেরোর দুই ভবেন হালদার লেনের অস্তিত্ব কোথাও আছে কিনা বিজন ঘোষ জানে না।
অন্ধকারশূন্য ঘরে তার নিঃশব্দ হাসিটা গাল বেয়ে প্রায় কানের দিকে ছড়াচ্ছে। এখন। কলকাতায় এসে এই দেড় বছর ধরে এই গোছেরই একটা স্বপ্ন দেখেছিল যেন। স্বপ্নের গাছে বাস্তবের ফল সত্যিই ধরে?
বিজন ঘোষও হরিপদ কেরানীদেরই একজন। এই শূন্যঘরে যে মানসীর আনাগোনা, তারও প্রনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর…।
বিজন ঘোষ কোনদিন তার অস্তিত্ব টের না পেলেও প্রমীতা গুপ্ত পাচ্ছে।
পরিতাপ
আমার ধারণা, বিচারে লোকটার ফাসী হবে, নয়ত দ্বীপান্তর হবে।
দুটোর একটা যাতে হয় পুলিস সে চেষ্টায় সুতৎপর। এই তৎপরতার দরুনই মঙ্গলের সঙ্গে দেড় বছর বাদে আমার আবার যোগাযোগ।
পুলিসের তদন্তসাপেক্ষে ওকে যেখানে আটকে রাখা হয়েছে সেখানকার ভারপ্রাপ্ত অফিসারটির সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের আলাপ। কাগজের অফিসের চাকরির দরুন হোক বা ভদ্রলোক নাট্যরসিক এবং আমি লেখক বলে হোক, আলাপটা মোটামুটি অন্তরঙ্গমুখী। এঁর কাছে গেলে অনেক সময় লেখার মত অনেক বিচিত্র রসদ মেলে। তাঁর দখলের আবাসটিও আমার বাড়ি থেকে দূরে নয়।
সেদিন সকালে ভদ্রলোক আমার বাড়িতে হাজির। অবকাশ পেলে সাধারণত আমিই তার ওখানে গিয়ে থাকি। এসেই সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ মশাই, মঙ্গল দাস নামে একটা লোককে আপনি চিনতেন?
চট করে ওই নাম বা নামের কোন মুখ স্মরণে এলো না। ভেবে বললাম, মনে। পড়ছে না তো!
সে তো আপনার নাম খুব ফলাও করে বলল, আপনি নাকি তার অনেক উপকার করেছেন…তার বদলে সে আপনার কিছু উপকার করেছে–আপনার দামী ঘড়ি, দামী পেন, জামার সোনার বোতাম আর পকেটের কিছু টাকা নিয়ে সরে পড়েছিল।
মঙলা! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল প্রতি মাসের গোড়ায় পদ্মমণিকে টাকা পাঠাত যখন, প্রেরকের নাম মঙ্গল দাসই লেখা হত বটে। মণি-অর্ডার আমিই লিখে দিতাম। কিন্তু ওই নামে বোর্ডিংয়ের কেউ তাকে চিনত না। সকলেই হাঁক দিত মঙলা বলে। নতুন বোর্ডার এসে নাম জিজ্ঞাসা করলে ও নিজেও এই নামই বলত। আর দুদিন না যেতেই নতুন বোর্ডার টের পেত, মঙলা সেখানকার একটি বিশেষ চরিত্র–আর পাঁচটা চাকর-বাকরের মত হেলাফেলা বা অবজ্ঞার পাত্র নয়।
আমাদের বোর্ডিংয়ে বেকার বা আধা-বেকারের বাস ছিল না। সবাই মোটামুটি ভালো উপার্জনশীল। একবার এক আত্মাভিমানী প্রায়-নতুন বোর্ডারের মুখের ওপর ও কী একটা জবাব দিয়ে বসেছিল, ফলে ঠাস করে গালের ওপর এক চড়। জবাবে স্তব্ধ চোখে মঙলা তার দিকে চেয়ে ছিল শুধু। এই ঔদ্ধত্যের জন্যেও নবীন ভদ্রলোক। দ্বিতীয় দফা তেড়ে এসেছিল। তার আগেই অন্য বোর্ডাররা হাঁ-হাঁ করে ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলেছিল। তেমনি নিষ্পলক তার দিকে চেয়ে থেকে মঙলা শুধু বলেছিল, এখন থেকে নিজের জন্য আপনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন।
এই কথা শুনে আর অন্য বোর্ডারদের বিচলিত হাবভাব দেখে চাকরি-গর্বা আধা নতুন বোর্ডারটি মনে মনে ঘাবড়েছে। পরে সতীর্থদের মুখে মঙলা-সমাচার শুনে মুখ আমসি। সকলের এক কথা, করলেন কী মশায়, এখন সামলাবেন কী করে! ওর দলের কানে তো পৌঁছুল বলে!
ওর দল বলতে এই এলাকায় ওদের শ্রেণীর ছন্নছাড়াদের গোষ্ঠী। ওদের মধ্যে অনেকে বাড়ি আর হোটেলে বোর্ডিংয়ে চাকরি করে, অনেকে আবার কিছুই করে না, উপার্জনের আশায় নানা রকমের বাঁকা রাস্তায় ঘোরাফেরা করে। এ-রকম একটা দলের। ও মাতব্বর হয়ে বসল কী করে সঠিক খবর রাখি না। রোজ দুপুরে সামনের পার্কের একটা চাতালে ওদের জুয়ার আড্ডা বসে। আমার ধারণা, এই থেকেই মঙলা ওদের পাণ্ডা। গোড়ায় ওকে দুই-একবার সাবধান করেছি, তোমাকে পুলিশে ধরল বলে!
ও তাচ্ছিল্যভরে জবাব দিয়েছে, পুলিশ নিজের ক্ষেতি করবে কেন, তার ট্যাকেও দুপয়সা আসছে।
তবে ওই মঙলাই আমাকে আশ্বস্ত করেছিল, এখন আর সে জুয়া-টুয়া খেলে। না, আড্ডায় গিয়ে বসে এইমাত্র, নইলে ছোঁড়াগুলো নিজেদের মধ্যে কাটাকাটি খাওয়া খাওয়ি করে। একদিন সে ওদের থেকেও অনেক বড় বদমাস ছিল, এখন ভালো হতে চায় বলেই চাকরি করছে আর জুয়াখেলাও বলতে গেলে ছেড়েই দিয়েছে।
ওর এই সুমতির কিছু কিছু কারণ আমার জানা আছে। সেটা পরের প্রসঙ্গ। যাক, ওর সমাচার শোনার পরেও সেই আত্মাভিমানী নব্য বোর্ডারটি ভয় গোপন করে। ঝাঁঝিয়ে উঠতে চেষ্টা করেছিল, এ-রকম একটা রাফিয়ানকে বোর্ডিংয়ে রাখা হয়েছে। কেন–পত্রপাঠ তাড়িয়ে দেওয়া উচিত আর পুলিসেও একটা খবর দিয়ে রাখা উচিত।
একজন বলে উঠেছিল, উচিত কাজ নিয়ে মাথা ঘামানোর আগে নিজের মাথাখানা। বাঁচাবার কথা ভাবুন মশাই! বলা নেই কওয়া নেই, আপনি গায়ে হাত তুলতেই বা গেলেন কেন? এখনো সেই রামরাজত্বে আছেন ভাবেন?
সন্ধ্যেনাগাদ সতীর্থরাই তাকে আমার কাছে আসার পরামর্শ দিয়ে পাঠিয়েছে বোঝা। গেল। তাদের ধারণা, এরপর আমিই বলে-কয়ে মঙলার মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারি, অন্যথায় বিপদ অনিবার্য। ভয়ে ত্রাসে ভদ্রলোক মুষড়ে পড়েছে। অগত্যা মঙ্গলাকে ঘরে ডেকে বললাম, বাবু একটা অন্যায় কাজই করে ফেলেছেন, তুমি কিছু মনে রেখো না।
ড্যাবড্যাব করে খানিক মুখের দিকে চেয়ে থেকে ও জিজ্ঞেস করল, আপনি ওনার মঙ্গল চান?
না চাইলে তোমাকে ডাকলাম কেন?
চাহিবেন বৈকি বাবু, আপনিও ভদ্র লোক, আর একজন ভদ্রলোক একটা ছোটলোকের গায়ে হাত তুলেছে এ আর এমন কী কথা!
ফাঁকে পেলে ও আমাকে অনেক রকমের নীতিকথা শোনায়! কিন্তু এ কথার ধার অন্যরকম। মুখে বিরক্তির ভাব এনে বললাম, তাহলে কী করতে হবে এখন?
আড়চোখে একবার ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে ও জবাব দিল, ওঁর ভালো চাইলে কাল সকালের মধ্যে ওঁকে এখেন থেকে চলে যেতে বলুন।
রাগ হচ্ছিল বটে, কিন্তু মঙলাকে যে চেনে সে নির্বোধের মতো রাগ করবে না। পাংশুমূর্তি ভদ্রলোকের দিকে ফিরে আমি বললাম, ঠিক আছে, কাল সকালে আমি আপনি দুজনেই চলে যাব এখান থেকে!
এবারে মঙলা থমকালো একটু। থমথমে মুখে একবার আমার দিকে আর একবার ভদ্রলোকের দিকে তাকালো। তারপর হনহন করে দরজার ওধারে চলে গিয়েও অসহিষ্ণু ক্ষোভে ফিরে এলো আবার। শরণাপন্ন বোর্ডারটির দিকে চেয়ে গরগর করে উঠল, দিনকাল খারাপ, হাত নিশপিশ করলেও হাত দুটোকে বশে রাখতে শেখেন! আমার দিকে ফিরে অভিমানহত ঝঝে বলে গেল, গরিবের আপনজন কেউ নেই, সবাইকেই জানা আছে আমার-কাউকেই যেতে হবে না এখান থেকে।
এই মঙলা!
.
বিস্ময় চেপে পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞেস করলাম, চুরির চার্জ নাকি?
মাথা নেড়ে পুলিশ অফিসার জবাব দিলেন, একেবারে প্রাণ চুরি-মার্ডার চার্জ!
চমকে উঠলাম। নিজের অগোচরে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কী সর্বনাশ, গৌরী দাসীকে?
ভদ্রলোক নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসলেন।–আপনি জানলেন কী করে?
আমি বিমূঢ়। কী ফ্যাসাদ ঘটালাম কে জানে।
পুলিশ অফিসারটির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মুহূর্তের জন্য। তারপর মুখে হাসি ঝরল। বললেন, যা জানেন, বন্ধু হিসেবে খোলাখুলি বলুন–তাতে বরং লোকটার কিছু উপকার হতে পারে… এভিডেন্স যা, তাতে ওর অব্যাহতির আশা কম। অথচ লোকটার। হাবভাব কেমন পিকিউলিয়ার…নট লাইক এ সীজৰ্ড ক্রিমিন্যাল। কিন্তু মার্ডার শুনেই আপনার গৌরী দাসীর নাম মনে এলো কেন?
সত্যি জবাবই দিলাম–বোর্ডিং-এ থাকতে ও শাসাতে ওই একটা মেয়েছেলেকে ঠিক একদিন খুন করে বসবে! বলত, ভগবান যেন তার হাত থেকে ওকে রক্ষা করেন!
পুলিশ অফিসার বললেন, রক্ষা করেনি, ওই-গৌরী দাসীই তার নিজের বস্তিঘরে খুন হয়েছে। ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়ালেন। জরুরী কাজ পড়েছে, যেতে হবে…বিকেলের দিকে আমার অফিসে আসুন একবার, এ নিয়ে একটু আলাপ-আলোচনা করা যাবে। বোর্ডিংয়ের চাকরির আমলে কে ভালো চিনত জিজ্ঞেস করতে মঙ্গল দাস প্রথমেই আপনার নাম করল, আর আপনার কী কী চুরি করেছিল তাও কবুল করল। আপনি নাকি ইচ্ছে করলেই তাকে ধরাতে পারতেন, কিন্তু ধরান নি। ভয়ানক শ্রদ্ধা আপনার ওপর। আপনার সঙ্গে আমার খাতির আছে শুনেই একবার দেখা করিয়ে দেবার জন্য দুহাত জুড়ে আকৃতি। নিয়ম নেই, বাট আই মে ট্রাই, আসুন তো একবার বিকেলে
চোখের সামনে একদিনের ছবি ভেসে উঠল। বোর্ডিংয়ের বাজার সেদিন আমার হাতে। বাজার করে ফিরছিলাম–মঙলার দুহাতে দুটো বড় বোঝা, পিছনে মুটে! মঙলা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল।
অদূরে একটা ভিখিরি গোছের লোক তার সাত-আট বছরের একটা ছেলেকে বেদম মারছে। মার খেয়ে ছেলেটা ফুটপাতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, কিন্তু তবু বাপের রাগ কমছে না।
মঙলা হঠাৎ হনহন করে এগিয়ে গেল। তারপর হাতের বোঝা মাটিতে রেখে হাড়-জিরজিরে লোকটার ঝাকড়া চুলের মুঠি ধরে ঠাস ঠাস করে দুই গালে দুটো পেল্লায় চড়। কাছাকাছি যারা ছিল সকলে হতভম্ব, এমন কি যে লোকটা মার খেল সেও। দাঁতে দাঁত ঘষে মঙলা বলে উঠল, এ-সব ছেলে জন্মায় কেন,জন্মায় কেন পাজী শূওর কোথাকার!
লোকটার হাতে চারআনা পয়সা গুঁজে দিয়ে আমি মঙলাকে একরকম ঠেলে নিয়ে বোর্ডিংয়ে ফিরি।
বোর্ডিংয়ের মাসিক ফিস্টএর দিন সেটা। অতএব আনন্দের দিন। কিন্তু রাত পর্যন্ত মঙলার থমথমে মুখ। একসময় ওকে ঘরে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, সকালে ওভাবে লোকটাকে কেন মারল?
ও গুম হয়ে বসে রইল খানিক। তারপর হঠাৎ কপালে হাত দিয়ে বলল, এটা দেখেছেন?
কপালে মস্ত একটা পুরানো ক্ষতচিহ্ন। মুখের দিকে তাকালে ওটাই আগে চোখে পড়ে। বলে গেল, এই দশা ওর মা করেছে, তখন ওর বয়েস আট কি নয়। ফুটপাতে থাকত। ওর পাঁচ বছর বয়সে বাবা মারা যায়। তার পরের কবছরের মধ্যে আরো দুটো ভাই-বোন এসেছিল। তাদের বাবা কে মঙলা জানে না। মা ওকে যখন-তখন। ধরে বেদম ঠেঙাত। একদিন ও রাগ করে খাবার ফেলে দিয়েছিল বলে চুলের মুঠি ধরে মা ওকে মাটিতে ফেলে থেতলাতে লাগল। কপাল ফেটে চৌচির-রক্তে ভেসে গেল। মা ওকে সেদিন মেরেই ফেলত বোধহয়, অন্য লোকের জন্য পারেনি। মায়ের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে ও ছুটে পালিয়েছিল। কপালের ক্ষতের মধ্যে অনেক ময়লা ঢুকে যেতে শরীর বিষিয়ে গেছল। কদিন অজ্ঞান হয়ে ছিল জানে না, জ্ঞান হতে দেখে একটা হাসপাতালে পড়ে আছে। সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে আর ও মায়ের খোঁজ করেনি।
আজ ভিখারিটা তার ছেলেকে ওভাবে মারছিল যখন, ওর মনে হচ্ছিল সেই মার যেন ওর গায়ে পড়ছে।
এর পর দিনে দিনে মঙলার জীবনের আরো অনেক খবর আমি জেনেছিলাম। …দশ বছর বয়সে ও একজনের কাছে আশ্রয় পেয়েছিল। পেয়েছিল কারণ ও একটু একটু গান গাইতে পারত। ভিক্ষে পেতে সুবিধে হয় বলে মায়ের কাছে মার খেতে খেতে গান শিখতে হত। আশ্রয় যে দিয়েছিল তার নাম চিন্তমণি। তার কাছে ছ। বছরের একটা মেয়ে ছিল–নাম গৌরী। মোটাসোটা মেয়েটা দেখতে একেবারে মন্দ নয়। কার মেয়ে কোথাকার মেয়ে কেউ জানে না। মঙলা এসে জোটার পর চিন্তামণি ওদের হর-গৌরী সাজিয়ে পয়সা রোজগারের রাস্তা ধরল। রোজ রং মেখে সং সেজে ওদের পথে রেরুতে হত–হর-গৌরীর নাচ নাচতে হত, গাইতে হত সেই সঙ্গে, চিন্তামণি ভাঙা হারমোনিয়াম বাজাতো। রাস্তায় ছেলেমেয়েদের ভিড় জমে যেত, বাড়ির একতলর দোতলায় দাঁড়িয়ে মেয়েরা মজা দেখত, নাচগান শেষ হলে পয়সা ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিত।
এক-একদিন চিন্তামণির বেশ ভালো রোজগার হত। পরিশ্রম খুব হত, পায়ের। সুতো ছেঁড়ার দাখিল হত। কাহিল হয়ে পড়লে চিন্তামণি কষে ঠ্যাঙানি লাগত। তবু এই নেচেগেয়ে বেড়ানোটা ভারী পছন্দের জিনিস ছিল মঙলার। দশ থেকে আঠেরো এই আট বছর এমনি কেটেছে। তার পরেই গণ্ডগোলের সুত্রপাত। গৌরীর তখন চোদ্দ বছর বয়েস, কিন্তু দেখাতো সতের-আঠেরোর মতো। তার আশেপাশে বাজে লোক জুটতে লাগল। মঙলাও তখন কুসঙ্গে মেশা শুরু করেছে, তাই সবই সে বুঝতে পারে। আরো একটা বছর টেনেটুনে কাটানো গেল। তারপর আর গেল না–গেল না মঙর জন্যেই। পনের বছরের গৌরীর নাচ সকলে হাঁ করে গেলে, চোখে-মুখে। কুৎসিত ইঙ্গিত করে। অথচ তার মত ধাড়ী ছেলের নাচ যেন সকলের চক্ষুশূল, হেসে হেসে টিটকিরি দেয়। হর-গৌরী পালার মধ্যে দুজনে কাছাকাছি হলে সকলে হৈ-হৈ করে ওঠে।
ঘরে ফিরে মঙলা রাগ করে, আর গৌরী হি-হি করে হাসে। কখনো ফিরে আঁঝ। দেখিয়ে বলে, লোক অমন করবে না তো কি–গায়ে হাত দেবার সময় তুই আজকাল সাপটে ধ্বতে চাস আমাকে! কার চোখে ধুলো দিবি?
বেগতিক দেখলেই মঙলা ওকে ধরে মার লাগাতো। আর মার খেলেই গৌরী ফুঁসে উঠত। ফলে আরো বেশি মার খেত। মেয়ে সেয়ানা হয়ে উঠেছে। বেশ। ফাঁক পেলে বাজে ছেলের সঙ্গে ফিসফিস গুজগুজ করে। ওদিকে নাচ প্রায় হু, খাওয়া জোটে না। মঙলা এখানে-সেখানে বা কারখানায় কাজের। ধান্ধায় বেড়ায়।
একদিন ঘরে ফিরে দেখে ঘর খালি। গৌরীও নেই, চিন্তামণিও নেই। এরপর ছবছর কেটেছে। এই ছবছর ধরেই মঙলা ওদের খুঁজেছে। ও তখন পঁচিশ বছরের জোয়ান। ওদের পেলে দুজনকেই খুন করত। না পাওয়ার আক্রোশে আরো বেশি। উচ্ছজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বয়েসকালের মেয়ে দেখলেই ওর শিরায় শিরায় আগুন জ্বলত। কারখানায় চাকরি করত–মদ খেত, জুয়া খেলত আর দুরন্ত আক্রোশে ব্যাভিচারের পাতাল চষে বেড়াতো।
কারখানায় কাজ করার সময় হারানের বউ পদ্মর সঙ্গে যোগাযোগ। হারান কলে কাটা পড়ে মরেছে। তার বউটা রোজগারের আশায় আসে। বেশ সুশ্রী মেয়ে। অনেকেরই চোখ গেছে তার দিকে। কিন্তু মঙলার চোখও আটকেছে যখন, কারো ঘাড়ে দুটো মাথা নেই যে পদ্মর দিকে এগোবে।
কিছুদিনের ঘনিষ্ঠতার পর পদ্ম ওর জুলুমে পড়ে সেই রাতে ওকে ওর ঘরে আসতে বলল। অল্পস্বল্প নেশা করে মঙলা ওর ঘরে গেল। বেশি নেশা করলে আনন্দ মাটি। মাথায় আর এক ক্ষুধার আগুন জ্বলছে বলে সময়ের একটু আগেই গিয়ে পৌঁছুল।
ঘরে পা দিয়েই হতভম্ব সে। পদ্ম ভূঁয়ে লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে। সে কি কান্না! তার বুকের কাছে হারানের একটা পুরনো ফোটো। অদূরে একটা কচি ছেলে আর একটা কচি মেয়ে বসে বোবা-বিস্ময়ে মায়ের বুকফাটা কান্না দেখছে।
মুহূর্তের মধ্যে মঙলা কেমন যেন হয়ে গেল। পদ্মকে জেরা করে শুনল, হারান একদিন তাকে পথের থেকে ঘরে এনে তুলেছিল। মঙলা পাথর! মনে পড়ল, মায়ের সঙ্গে রাস্তায় রাত কাটতো যখন, তারও বোন ছিল একটা। এ সে-ই কিনা কে জানে! ঠিক সে না হোক, সেই রকমই একজন।
সেই থেকে মঙলা অন্য মানুষ। একে একে অনেক ছেড়েছে তারপর থেকে। কারখানার চাকরিও ছেড়েছে। না ছাড়লে পাতাল তাকে টানত। সেই বোর্ডিংয়ে চাকরি নিয়েছিল। পদ্মকে আর ছেলেমেয়ে দুটোকে হারানের দেশের ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছিল। মাসের শেষে আমাকে দিয়ে যে মণি-অর্ডার ফর্ম লিখিয়ে টাকা পাঠাতো, সে ওই পদ্মর কাছে।
ওর দুর্ভাগ্য, তাই ওই সময় গৌরীর সঙ্গে আবার দেখা। পথে দেখা প্রথমে হঠাৎ একদিন চিন্তামণির সঙ্গে। ওই বয়সেই চিন্তামণি বুড়িয়ে গেছে। হাঁপ-রোগে ভুগছে। মাথার চুল সাদা। মঙলাকে সে-ই তার বস্তিঘরে টেনে নিয়ে গেছে।
হা, মঙলা যা ভাবতে পারেনি তাই হয়েছে। মঙলা ভেবেছিল পুঁজি হাতছাড়া হবার ভয়ে চিন্তামণি গৌরীকে সরিয়েছিল। গৌরী ওর পুঁজি। কিন্তু তা নয়, গৌরীকে ও-ই জোর করে বিয়ে করেছে। গৌরীর থেকে চিন্তামণির বয়েস কম কারে এক-কুড়ি বেশি। কিন্তু ষোল বছরের মেয়েটাকে ও নিজেই খেয়েছে। তারপর সাত বছর কাটতে এই হাল।
গৌরীর দিকে প্রথম প্রথম মঙলা চোখ তুলে তাকাতে পারেনি। যৌবনেরই আগুন যেন ওর সঙ্গে বাসা বেঁধেছে। নড়লে-চড়লে ঝলসে ওঠে। হাসলে পরে উছলে পড়ে।
ঘরে একটা তিন বছরের রোগাটে ছেলে। গৌরীর ছেলে। বোবা-মূর্তি মঙলা। তাকেই একটু আদর করছিল, চিন্তামণি তখন বাইরে চা বানাচ্ছিল–সেই ফাঁকে গৌরী বেশ কাছে এসে কোমরে দুহাত দিয়ে ছদ্ম ভ্রুকুটি করে সকৌতুকে তাকে দেখছিল। ছেলেকে আদর করতে দেখে হেসে গুনগুন করে গেয়ে উঠেছিল, হায় গো হায়, রাই না পাই, দুধের সাধ ঘোলে মেটাই।
সেই থেকে মঙলার মাথায় আবার আগুন জ্বলতে শুরু করেছিল। প্রায়ই ইচ্ছে হত চিন্তামণিকে খতম করে দিয়ে সবদিক পরিষ্কার করে ফেলে।
কিন্তু দেখা হলেই হেঁপো রোগী চিন্তামণি ওর কাছে দুঃখ করত। বলত, গৌরী তাকে দেখতে পারে না, এমন কি ওর ওপর রাগে রোগা ছেলেটাকে পর্যন্ত দেখতে পারে না। চিন্তামণির ধারণা, একটা পালাগানের দল ওকে না করে দিতে পারলে আর বেশিদিন ওকে ধরে রাখা যাবে না। ছেলেবেলার সেই ঝোঁক গৌরীর এখনও কাটেনি। এক বাড়িতে গৌরী এখন দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনটে ছেলেমেয়ে রাখার কাজ করে। সেই বাবুটির বউ নেই। বাবুর মতলব ভাল নয় বুঝেও গৌরী তাকে আসকারা দেয়। কিছু বললে উল্টে শাসায়, শিগগীরই পালাগানের দল না করে দিলে ও যার সঙ্গে খুশি তার সঙ্গে চলে যাবে।
কিন্তু পালাগানের দল খোলার মত টাকা চিন্তামণি পাবে কোথায়?
রঙ্গ করে গৌরী একদিন চিন্তামণির সামনেই মঙলাকে বলেছিল, তুমি যোগাড় করে দাও না টাকা, তুমি তো আমার প্রথম পক্ষের শিবঠাকুর গো, ভাগে-সাগে না হয় দুজনেরই ঘর করা যাবে। এমন কী দোষের, দ্রৌপদী তো পাঁচজনের ঘর করত। বলেই খিলখিল হাসি। এত হেসেছিল বলেই কথাটায় তেমন দোষ ধরেনি চিন্তামণি। কিন্তু মঙলার মাথার আর বুকের জ্বলুনি বেড়েই গেছল।
.
একদিন সকাল থেকে মঙলার দেখা নেই। বোর্ডিংয়ে ফিরল সন্ধ্যার পর। উসকো খুসকো মূর্তি। দেখলেই বোঝা যায় বিশেষ কিছু ঘটেছে। রাত্রিতে ওকে ঘরে ডেকে এনে ব্যাপার শুনলাম। গৌরী তার বাবুর বাক্স থেকে তিনশ টাকা চুরি করে চিন্তামণির হাতে দিয়েছে। প্ল্যান ছিল ভোররাতে ওরা পালাবে, তারপর দূরে কোথাও গিয়ে ওই টাকা দিয়ে পালাগানের দল গড়বে। কিন্তু মঙলার মতে চিন্তামণি বুদ্ধিমান লোক, সে জানে পালাগানের দল হোক বা না হোক, গৌরী একদিন তাকে ছেড়ে চলে যাবেই। তাই কড়কড়ে তিনশ টাকা হাতে পেয়ে মাঝরাতে উঠে সে একাই পালিয়েছে। ওদিকে বাবু পুলিশে খবর দিতে তারা এসে গৌরীকে টানাহেঁচড়া করছে। গৌরী অবশ্য স্বীকার করেনি, কিন্তু স্বীকার না করে যাবে কোথায়? বাবুর বাড়ি গিয়ে তার হাতেপায়ে ধরেছিল, বাবু শেষ পর্যন্ত বলেছে টাকা পেলে ফয়সলা করে নেবে।
তারপর?
তারপর মঙলা গৌরীর ঘরে গেছে। এলোপাথারি কিল-চড় মেরেছে তাকে। মেরে এখানে চলে এসেছে। বলল, ও আমার হাতে একদিন ঠিক খুন হবে। একথা আগেও বলেছে।
পরদিন আমার ঘড়ি, পেন আর সোনার বোতাম চুরি এবং মঙলা নিখাঁজ।
পুলিশ অফিসারকে মঙলা ঠিকই বলেছে, একটু তৎপর হয়ে গৌরী দাসীর বস্তি ঘরের আশেপাশে পুলিশ মোতায়েন করলেই আমি ওকে ধরতে পারতুম।
.
বিকেলে পুলিশ অফিসারের ঘরে গেলাম। তিনি বললেন, আপনার মঙ্গল দাস লোকটার মশাই মেজাজ এখনও তিরিক্ষি। কবুল করবার ফিকিরে ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা হচ্ছে কিনা। ও তার জবাবে খানিক চুপ করে থেকে আমাকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, মানুষ মরলে ফিরে আবার জন্মায় কিনা। বুঝুন ঠেলা–অর্থাৎ আবার জন্মালে আবার ও গৌরী দাসীকে খুন করবে!
একটু বাদে মঙলাকে আমার সামনে এনে হাজির করা হল। তার হাতে শেকল, পায়ে বেড়ি, কোমরে দড়ি। আমি আঁতকে উঠলাম-প্রেত-মূর্তি যেন!
অফিসার আমাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী, চিনতে পারো?
জবাবে যতটা সম্ভব ঝুঁকে শেকল-বাঁধা-হাত কপালে ঠেকিয়ে আমাকে প্রণাম করল! আমাকে অবাক করে দিয়ে পুলিশ অফিসার উঠে দাঁড়িয়ে ওকে বললেন, বাবুর সঙ্গে কথা বল, আমি একটু কাজ সেরে আসি–কিছু ভয় নেই।
ঘর ফাঁকা। বাইরে অবশ্য প্রহরী মোতায়েন বলে ধারণা আমার। তাছাড়া এ রকম অবস্থায় ওই একটা সামনের দরজা দিয়ে কারো পালাবার প্রশ্ন ওঠে না। তবু কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।
বাবু ভালো আছেন?
আমি সচকিত।-হ্যাঁ।…কিন্তু এ কী হলো!
জবাবে ও ওপরের দিকে ঘাড় উঁচিয়ে তাকাল একবার। তারপর বিড়বিড় করে বলল, সবই অদেষ্ট। একটু বাদেই ওর গর্তের চোখ দুটোতে আগ্রহের ছোঁয়া লাগল। –আচ্ছা বাবু, মানুষ মরলে আবার জন্মায়?
পুলিশ অফিসার এ প্রশ্নের যাই তাৎপর্য বুঝুন, আমি বুঝতে পারলাম না। জানি না …কেন বল তো?
জবাব দিল না। চুপ করে খানিক ভাবল কি। তারপর অনুনয়ের সুরে বলল, বাবু, আপনার কাছেও আমি অপরাধ করেছি, তবু দয়া করে আপনি আমাকে ক্ষমা করেছেন। আর একটুখানি দয়া চাইব বাবু…?
আমি জিজ্ঞাসু।
মঙলা বলল, গৌরীর রোগা ছেলেটাকে ওরা অনাথ আশ্রমে রেখেছে। শুনলাম…আমার কিছু টাকা আছে, হক্কের টাকা, সেটা যাতে ওই ছেলেটার ভালোর জন্যে খরচ হয় আপনি সে ব্যবস্থা করে দেবেন–দেবেন?
বললাম, আচ্ছা সে হবেখন, আগে তো কেটেস হোক।
এরপর দুচার কথায় ব্যাপারটা শোনা গেল।…চুরির দায় থেকে খালাস পেয়ে গৌরী যেন কেনা দাসী হয়ে গেল মঙলার। নিজেকে ওর কাছে বিলিয়ে দিয়ে ওর নেশা ধরিয়ে দিল। মঙলা দূরের এক কলে কাজ নিয়েছিল, প্রতিজ্ঞা করেছিল, আমি ওকে পুলিশে ধরিয়ে দিলাম না বলেই ও রোজগার করে চুরির দেনা শোধ করবে। হপ্তার ছুটির দিনে গৌরীর বস্তিতে আসত, একদিন থেকে আবার চলে যেত।
কিন্তু গৌরী আসলে ওকে ভালবাসত না, ভয় করত। ভিতরে ভিতরে যে অন্য লোক জুটিয়েছে সেটা বোঝা গেল বছর না ঘুরতে। দুই-একবার ধরা পড়ে ওর হাতে বেদম মার খেল গৌরী। মার খেয়ে কিছুদিন ঠাণ্ডা হয়ে থাকে, তারপর আবার বেচাল শুরু হয়। একবার খাওয়ার দোষে ওর রোগা ছেলেটা মরমর, ভাবনা-চিন্তায় মঙলা রাতে ফ্যাক্টরী থেকে পালিয়ে বস্তিতে এসে দেখে সেই বিপদের দিনেও রাতের আঁধারে বেড়ার গায়ে দাঁড়িয়ে বাবুগোছের একটা লোকের সঙ্গে গৌরী ফিসফিস করছে। ওর সাড়া পেয়েই লোকটা পালিয়ে গেল।
সেই রাতে হাড়ভাঙা মার খেয়েও মঙলা দেখেছে, গৌরীর দুচোখ বাঘিনীর মতো জ্বলছে। এর কমাসের মধ্যে মঙলা যে করেই হোক স্থির বুঝেছিল, গৌরী ওকে ছেড়ে পালাবে। বুঝেছিল, কারো সঙ্গে পালাবার ষড়যন্ত্র পাকা করে এনেছে। এই পর্যন্ত বলে। মঙলা থামল।
আমি বলে উঠলাম, ও-রকম একটা মেয়ের জন্য নিজের এতবড় বিপদ ডেকে আনলে?
আবার একটু চুপ করে থেকে মঙলা বিড়বিড় করে জবাব দিল, কোন মেয়ের জন্য নয় বাবু, গৌরীকে খুন না করলে ওর হাতে একটা শিশু খুন হত। নিজের ছেলেটাই সব থেকে বড় কাটা, ওকে একেবারে সরিয়ে দিয়ে পালাবার মতলব ভেজেছিল ওরা।…আগেরবারে খাবারের সঙ্গে বিষও গৌরীর ওই লোকই দিয়েছিল।..বুকে ছোরা বসাবার পর চোখের জলে ভেসে গৌরী সব স্বীকার করে গেছে।
.
ঘরে পুলিশ অফিসারের সামনে বোকার মতো আমি বসে। উনি বললেন, এ ঘরের আপনাদের সব কথা ওদিক থেকে শোনার ব্যবস্থা আমি আগেই করে রেখেছিলাম। ..ভেরি স্যাড ইনডিড়!
অন্যমনস্কের মতো বাড়ি ফিরছি। পর পর কতগুলো দৃশ্য আমার চোখের সামনে। ভাসছে।…একটা ভিখিরি তার ছেলেকে মারছে দেখে হাতের মোট নামিয়ে ক্ষিপ্ত আক্রোশে মঙলা তাকে মেরে বসল।…আদিম রিপুর তাড়নায় পদ্মর ঘরে গিয়ে সেই কান্না দেখে, আর তার থেকেও বেশি–সেখানে দুটো অসহায় নির্বাক শিশুমূর্তি দেখে ওই উচ্চুঙ্খল মঙলার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল।…আর তারপর, ওই মঙলা আর একটা অসহায় শিশুর আসন্ন মৃত্যুভয়ে গৌরী দাসীকে খুনই করে বসল।… কেন, পথের ছেলে মঙ্গলা কি ওদের মধ্যে নিজেকেই দেখত?
চমকে উঠলাম। কানে যেন বিড়বিড় স্বরের একটা উৎসুক প্রশ্ন আঘাত করল।–আচ্ছা বাবু, মানুষ মরলে আবার জন্মায়?
…মঙলা আজীবন তার জম্মটাকে ঘৃণা করেছে। আবার একটা জন্মের অভিশাপ ও বহন করতে চায় না।
যৌবন
দুনিয়াখানা যৌবনের বশ।
এক বুড়ো প্রায়ই আক্ষেপ করত, আর বলো কেন ভায়া, দুনিয়া তার যৌবন যার।
ছেলেবেলায় এই যৌবনটির জন্য ভিতরে ভিতরে একটা লোভনীয় প্রতীক্ষা ছিল। বোধহয় সকলেরই থাকে। কিন্তু সময়ের বেড়া বাঁধা এই রম্য বাগিচায় পা ফেলার পর তার অনেক চটক চোখে পড়ে না। যাই হোক, ওই দুর্লভ গণ্ডীর মধ্যে বিচরণকালে তার মহিমা সম্পর্কে আমি নিজে অন্তত ধ্ব সচেতন ছিলাম না।
ক্রমে প্রৌঢ় ব্যবধানে সরে আসার পর আজ আবার সকৌতুকে চেয়ে চেয়ে দেখছি, যৌবন চটকদার বস্তু বটে। শুধু তাই নয়, দি ওয়ার্লর্ড ইজ ফর দি ইয়ং–সেই বুড়োর ভাষায়, দুনিয়া তার যৌবন যার।
এক নামজাদা দার্শনিক বলে গেছেন, যৌবন অনেক সময় কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, কিন্তু কদাপি ধী-শূন্য নয়। সর্বকৃত্রিমতার ওপর তার তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি–সে ধোঁকা বা ফাঁকি ধরতে জানে। কিন্তু আজকের বাস্তব দুনিয়ার দার্শনিক এই বাসি প্রসঙ্গ নিয়ে আদৌ মাথা ঘামাবেন কিনা সন্দেহ। তিনি বরং উত্তর-যৌবন সম্পর্কে কিছু দর্শন বচন। শোনাতে পারেন। কারণ এ-যুগের এটাই বড় সমস্যা।
কেন?
কারণ দি ওয়ার্লর্ড ইজ ফর দি ইয়ং। যৌবন যার দুনিয়া তার। এতে দ্বিমত কেউ নয়।
অতএব আজকের দার্শনিক বলেন যদি কিছু, যৌবনের বদলে সম্প্রসারিত যৌবনের কথা বলবেন। অর্থাৎ কাল ফুরালেও যে যৌবনের বহিরঙ্গ অনেক কাল পর্যন্ত অটুট রাখা যায়–তার কথা। আর বলবেন বোধ হয় একেবারে উল্টো কথাই। বলবেন, টেনে বাড়ানো এ যৌবন ধী-শূন্য যদিবা, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য কদাপি নয়। সর্বকৃত্রিমতা আড়াল করার প্রতি তার তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিধোঁকা আর ফাঁকি তার একমাত্র পুঁজি।
খবরের কাগজে সেদিন একটা কার্টুন দেখে আপনারা অনেকে হাসাহাসি করেছেন জানি।…এক ভিড়ের ট্রাম থেকে একজন মহিলা নেবে যাচ্ছেন, তার চুলের (পরচুলের) বোঝা এক ভদ্রলোকের ছাতায় আটকে আছে, আর ভদ্রলোক তাকে চেঁচিয়ে ডাকছেন, ও ম্যাডাম, আপনার সব চুল যে আমার ছাতায় আটকে থাকল, নিয়ে যান, নিয়ে যান! ২০০
যাঁরা হেসেছেন তারা হেসেছেন, কিন্তু আমার ধারণা, যদি কোনো ম্যাডামের বরাতে অমন দুর্দৈব ঘটেই, তার পুঁজি খোয়ানোর দুঃখে আজকের দিনে কাদবার লোকেরও অভাব হবে না।
যাক, আমি কোনো গুরু-গম্ভীর তত্ত্ব বিস্তারে বসিনি। যৌবন আগলে রাখার প্রেরণা বা তাড়নার বহু বিচিত্র নজির সকলেই হামেশা দেখছেন। অবকাশ সময়ে আমিও দেখি। আমার দেখার রঙ্গপট একটি হাল-ফ্যাশনের চুলছাটার সেলুন। নাম প্রসাধনী। প্রসাধনীর হেড কারিগর যে, মালিকও সেই। নাম অমল, বয়েস এখন তিরিশ-বত্রিশ হবে। চৌকস চটপটে ছেলে। আমি তাকে গত বারো বছর ধরে দেখছি। তখন বাড়িতে এসে চুল ছেটে দিয়ে যেত। নিজের উদ্যমে দোকান করেছে, তারপর কবছরের মধ্যে সেটাকে এমন ঝকঝকে করে তুলেছে। আশপাশের দুটো সেলুন কমপিটিশনে টিকতে না পেরে উঠে গেছে। তাদের বাছাই-করা তিনটি কারিগর প্রসাধনীতে কাজ পেয়েছে। অমলের আশা অদূর ভবিষ্যতে সেলুনটাকে সে এয়ার কণ্ডিশন করে ফেলতে পারবে। আর তার একটা বড় খেদ, এ লাইনে একটিও দিশি মেয়ে-কারিগর মেলে না। তাহলে আলাদা একটু পার্টিশন করে মেয়েদের ব্যবস্থাও রাখত। দোকান জমজমাট হত তাহলে। এ তো আর সাহেব-পাড়ার দোকান নয় যে মেয়েরা এসে পুরুষ কারিগরের হাতে। চুলের বোঝা ছেড়ে দেবে! মেয়েরা না থাকলে কোনো ব্যাপারই ঠিক কমপ্লিট হয় না, কী বলেন সার?
ওর হাত যেমন চলে, রসালো জিভখানাও তেমনি অবিরাম নড়ে। আমাকে দেখলে আরো বেশি নড়ে। গল্প উপন্যাস লিখি ও জানে। একটু-আধটু পড়ে। তাই দেখামাত্র অন্য। খদ্দেরদের শুনিয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানায়। তারপর সোৎসাহে বলে, আপনার অমুক লেখাটা পড়ছি স্যার। ওমুক বইটা খুঁজছি, বা আপনার ওমুক ছবিটা দেখলাম, হাই ক্লাস!
গোড়ায় গোড়ায় বিড়ম্বনা বোধ করতাম, বিরক্তও হতাম। কিন্তু ও সেটাও খুব। সহজেই বুঝত। তাই ফাঁক পেলেই গলা খাটো করে বলত, কিছু মনে করবেন না। স্যার, এরকম বললে আপনার তো কোনো ক্ষতি হয় না, কিন্তু আমার বড় উপকার। হয়–কতজন এসে আপনার কথা জিজ্ঞেস করে আপনি জানেন না স্যার।
প্রসাধন-কলা ছেড়ে তোষামোদ-কলাতেও লোকটা যে কম পটু নয়, এ বোধহয়। ওর শত্রুও স্বীকার করবে।
ওর বচনের জ্বালায় হোক বা ভিড় এড়ানোর জন্যে হোক, ইদানীং প্রতি মাসে। আমি রাত্রের নিরিবিলিতে আসি। তখনো যে খদ্দের একেবারে থাকে না এমন নয়, তবু অপেক্ষাকৃত কমই থাকে। যাই হোক, এখান থেকে মানুষের যৌবনপ্রীতির অনেক সকৌতুক নজির আমি দেখছি। আর এই দেখাটুকু লক্ষ্য করেই অমল খদ্দেরদের অনেক মজাদার কাণ্ডকারখানা আমাকে শোনায়। এই নিয়ে আমি একবার একটা হাসির গল্প। লিখেছিলাম। এরপর থেকে ওকে আর পায় কে! রসদ যোগাবার তরল আনন্দে ও আপনা থেকেই মুখর হয়ে ওঠে।
সেদিন রাত নটা নাগাদ গিয়ে দেখি, অমলের দোরে ঝকঝকে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে। ভিতরে অমল অপরিমিত মনোযোগ সহকারে এক সৌখিন ভদ্রলোকের চুলে কলপ লাগাচ্ছে। বলতে ভুলে গেছি, সাদা চুল পরিপাটিভাবে তকতকে কালো করাটাও প্রসাধনীর এক বড় আকর্ষণ। অমল বলে, এ কাজে ও স্পেশ্যাল ট্রেনিং নিয়েছে। চুল কালো করার মাশুল দু-টাকার থেকে পাঁচ টাকা–অর্থ্যাৎ খদ্দের বুঝে যেমন আদায় করা যায়। ব্যাপার লক্ষ্য করেছি প্রায় একই, শুধু একটু যত্ন-আত্তি আর তোষামোদের যা তফাত।
ভদ্রলোককে দেখে আর অমলের সুতৎপর তন্ময় মনোযোগ দেখে বুঝলাম, পাঁচ টাকার খদ্দের তো বটেই, বেশিও হতে পারে। ভদ্রলোকের বয়েস ষাটের কাছাকাছি। মোটামুটি সুপুরষ। হাতে সোনার ঘড়ি, আঙুলে মুক্তো আর নীলার আংটি, জামায় হারের বোতাম।
ভদ্রলোকের চুল কতটা সাদা ছিল সঠিক বোঝা গেল না। কারণ কলপ-বিন্যাসপর্ব প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। এখন অমল যা করছে সেটা বাড়তি। স্ফীত অঙ্কের কিছু প্রাপ্তির আশা তার। আমাকে দেখেই চোখের ইশারায় একটু অপেক্ষা করতে বলল, এবং অন্য কারিগর আমার দিকে এগিয়ে আসতে ইশারায় তাকেও নিষেধ করল। অর্থাৎ হাত খালি হলে সে নিজেই কাজ ধরবে বুঝলাম, আমাকে শোনানোর মতই কিছু রসদ তার কাছে জমা আছে।
আরো মিনিট দশেকের মধ্যে ওদিকের কেশবিন্যাস শেষ। অমল তাড়াতাড়ি এগিয়ে। গিয়ে পুশ-ডোর ঠেলে দাঁড়িয়ে আরো একটু বাড়তি সম্ভ্রম দেখালো। ভদ্রলোক পকেট থেকে বড়সড় মানিব্যাগ বার করতে করতে পুশ-ডোরের ওধারে চলে গেলেন।
দরজা ঠেলে অমল আবার ফিরে আসতে দেখি চাপা খুশিতে তার মুখখানা ডগমগ করছে। হাতের দশটাকার নোটখানা ভাজ করে কাঠের বাক্সে রাখতে রাখতে সামনের দেয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকালো একবার। তারপর দ্বিতীয় কর্মচারীটিকে বলল, সাড়ে নটা বেজে গেছে, এই রাতে আর কেউ আসবে না, তুমি যাও।
আমার গলায় বুকে কাপড়ের এপ্রন জড়িয়ে চিরুনি কাচি হাতে পিছনে এসে। দাঁড়াল।–স্যার, এই যে ভদ্রলাকটি চলে গেলেন…চিনলেন?
কাঁচি চলছে, মাথা নাড়ার উপায় নেই, বললাম, না।
–মস্ত লোক, আপনার তো চেনার কথা। জণ্ড দত্ত…থিয়েটার কোম্পানীর মালিক।
নামটা চেনা। ওই রাজ্যের মস্ত লোকই বটে।–তোমার খদ্দের হয়েছেন?
–হ্যাঁ, দুমাস ধরে। পাকা হাতের কলপ মাসে একবার লাগালেই চলে, কিন্তু উনি পনের দিন অন্তর অন্তর আসছেন–এই দুমাসে চারবার এলেন।
আমি নিরীহ প্রশ্ন ছুঁড়লাম, কেন, চুল খুব বেশি সাদা?
–সাদাই বটে, তবে ভয়ে আর অশান্তিতে ভেতরটা আরো বেশি সাদা, বুঝলেন?
পরের বিশ মিনিটের মধ্যে বুঝতে আর কিছু বাকি থাকল না। অমল বেশ রসিয়ে সাদা চুলের ভয় আর অশান্তির ব্যাপারটার বিস্তার শুরু করল। তার সারমর্ম: জঙ দত্তর বয়েস এখন ষাট ছুঁয়েছে। তার চারটে বাড়ি তিনটে গাড়ি আর অঢেল টাকা। অবস্থাজনিত আনুষঙ্গিক গুণাবলীও আছে। তার মধ্যে একটি সত্যিকারের গুণও অস্বীকার করা যায় না। নিজের একটি ছোট ভাই আছে, নাম সুবল দত্ত-কম করে কুড়ি বছরের ছোট তার থেকে। এই ভাইটিকে বাপের মত মানুষ করেছেন তিনি, সত্যিই ভালবাসেন তাঁকে। বিষম গোল বাধল প্রিয়বালা আসার পর থেকে।
–প্রিয়বালাকে দেখেছেন নিশ্চয় স্যার! ওঃ। স্টেজে ঢোকে যখন সে তামাম হলখানার হাওয়া বদলে যায়!
দুমাস হল প্রিয়বালা জগুবাবুর থিয়েটারে যোগ দিয়েছে। পশ্চিমের ডাটালো মেয়ে, আগে কেউ তাকে কলকাতার কোনো থিয়েটারে দেখেনি। সেই থেকে জগুবাবু অমলের খদ্দের।
ওই প্রিয়বালা জগুবাবুর চোখের মণি। বাড়ি-ঘর ছেড়ে দিনরাত তার কাছেই পড়ে থাকতেন। কিন্তু ফ্যাসাদ বাঁধল আদরের ছোট ভাই সুবল দত্তকে নিয়ে। সেও প্রিয়বালার প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠেতে লাগল। ফলে রাগে দুঃখে নিজের মাথার চুল ছেড়েন জগু দত্ত। ষাট বছরের সঙ্গে চল্লিশ বছরের রেষারেষি। ওদিকে উদার হয়ে। ভাইটিকে বেশ একটা মোটা অঙ্কের টাকা অনেক আগেই দিয়ে বসেছিলেন। তার বিষ-গাছ গজাচ্ছে এখন। শোনা যাচ্ছে, সেই টাকা দিয়ে সুবল দত্ত প্রিয়বালাকে নিয়ে আলাদা থিয়েটার খুলবে।
–জগু দত্তর বন্দুক আছে স্যার, বুঝলেন। আর তার মাথায়ও রক্ত চড়েই আছে। একবার ভাবেন, ভাইকে গুলী করে মারবেন, আর একবার ভাবেন প্রিয়বালাকে।
…আমার মনে হয়, ওই বন্দুক দিয়ে শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক নিজের মাথারই খুলি ওড়াবেন…কি বলেন স্যার?
আমি কিছু বলিনি। কিছুদিন বাদে ভেবে-চিন্তে আর রাখা-ঢাকা করে একটা মামুলী গল্প লিখেছিলাম। সেই প্রেমের গল্পে ষাট বছরের সঙ্গে চল্লিশ বছরের রেষারেষিতে স্থল দৃষ্টিতে চল্লিশ বছরকেই জিতিয়ে দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে হৃদয়ের দিক থেকে ষাট বছরই অনেক বড় হয়ে উঠেছিল।
গল্পটা অমলের আদৌ পছন্দ হয়নি। সে বলেছে, এটা কি করলেন স্যার, ষাট বছর ওই অভিনেত্রীর জন্য তার চারটে বাড়ি আর তিনটে গাড়ির একটা করে খসালেই তো অনায়াসে তাকে হাতের মুঠোয় পুরতে পারত! আর জণ্ড দত্ত যদি কোনদিন জানতে পারে এই গল্পের খোরাক আমি জুগিয়েছি, আমাকে একেবারে জ্যান্ত পুঁততে চাইবে।
ভাবলাম, ষাট বছর জিতলে ও বোধহয় মোটা বকশিশই পেত তাঁর কাছ থেকে।
মাস দুই পরের কথা। প্রসাধনীতে চুকে সেই রাতে বিপরীত গোছের দৃশ্য দেখলাম। অর্থাৎ যেমনটি সচরাচর দেখা যায় না। রাতের নিরিবিলিতে মাথার একরাশ শনের মত সাদা চুল কালো করতে বসেছে নিতান্ত ক্লিষ্ট চেহারার একটি লোক। গায়ের রং রোদে-পোড়া কালচে-কপালের দুদিকে ফুটে ওঠা নীল শিরা দুটো দূর থেকে দেখা যায়। সর্বাঙ্গে দারিদ্র্য আর মেহেনতের ছাপ। পরনে তেলচিটে খাকি হাফপ্যান্ট, গায়ে বিবর্ণ একটা ফতুয়া। তবু বয়েস যাই হোক, দেহের কাঠামো তেমন শীর্ণ নয়।
– এ-হেন মূর্তির মাথার সাদা চুল কালো করার তাগিদটা ভারী অদ্ভুত লাগল। অমল তার ঝাকড়া চুলের মাথাটা নিজের দু-হাতের দখলে টেনে এনে গজগজ করে উঠেছে–স্থির হয়ে বসুন, অত ছটফট করলে কালোর ভেতর দিয়ে অনেক সাদা। চুল দাঁত বার করে হাসবে। এই সরব-দৃশ্যে আমার পদার্পণ।
অমল বিব্রত মুখ করে বলল, একটু বসুন সার, ভোলা চা খেতে গেছে, এলো। বলে—
ওর হাত জোড়া থাকলে ভোলাই আমার চুল কেটে থাকে। আমি মাথা নেড়ে অদূরে বসে সকৌতুকে অমলের ওই খদ্দেরটিকে নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। অমল সেটা লক্ষ্য করল এবং বার দুই-তিন আমার দিকে ফিরে তাকালো। বিরক্তি গিয়ে তার চোখেও বেশ সরস কৌতুক নেচে উঠেছে। সাদা চুলের গোছায় হাত চলাতে চালাতে সামনের আয়না দিয়ে লোকটার মুখখানা ভালো করে দেখছে আর চাপা খুশিতে দাঁতে করে নিজের ঠোঁটের কোণ কামড়াচ্ছে। এবারেও গল্প আছে কিছু, হাবভাবে অমল যেন সেটাই আমাকে বোঝাতে চাইছে।
ভোলা আসতেই গম্ভীর মুখে অমল তাকে ডাকলো, এই এদিকে আয়, এঁর কাজটা ধর–খুব ভালো করে বানিয়ে দিবি, চুল দিয়ে কালো জেল্লা বেরোয় যেন
সঙ্গে সঙ্গে লোকটাকে বলল, কিছু ভাবনা নেই মশায়, ও আমার থেকে অনেক ভালো কাজ করবে–জাপান থেকে চুল কালো করার ট্রেনিং নিয়ে এসেছে।
সংশয়-ভরা চোখে লোকটা একবার ভোলার দিকে তাকালো শুধু। কোনরকম প্রতিবাদ করল না।
অমল সোজা এগিয়ে গিয়ে লম্বা ঘরের ওধারের কোণের একেবারে শেষ চেয়ার আর আয়নার সামনে গিয়ে আমাকে ডাকল, ইদিকে আসুন স্যার
উঠে গেলাম। এই ব্যবধান রচনার উদ্দেশ্য বুঝেও বললাম, ওকে ছেড়ে এলে কেন, ভোলাই তো কাটতে পারত
আমার গলায় চাদর জড়াতে জড়াতে অস্ফুট একটা শব্দ বার করল গলা দিয়ে। তারপর চাপা ব্যঙ্গস্বরে বলল, দুটাকা রেট, দুদিন রাতদুপুরে এসে দরকষাকষি করে আজ দেড় টাকায় কাজ সেরে যাচ্ছে।
আমি ফিসফিস করে বলে উঠলাম, এমন অবস্থায় চুল কালো করার সখ!
–প্রাণের দায় যে। চুলে ক্লিপ চালিয়ে খাটো গলায় অমল লঘু উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করল, যেখানে মেয়েমানুষ সেখানেই গোল, বুঝলেন স্যার! খুব মজার ব্যাপার…আপনাকে বলব বলেই এদিকে নিয়ে এলাম…কিন্তু লিখতে গেলে এবারে আপনার পক্ষেও খুব মুশকিল হবে–
আড়চোখে যতটুকু সম্ভব ঘাড় ফিরিয়ে একবার লোকটার ওধারের দিকে তাকালাম। কোনো দিকে হুশ নেই, তন্ময় আগ্রহে আয়নায় নিজের সাদা চুলের ওপর ভোলার হাতের কসরৎ দেখছে।
চুলে কাঁচি চালাতে চালাতে অমল তেমনি চাপা গলায় আর চাপা আনন্দে মজার ব্যাপারটা বলে গেল।লোকটা কলে কাজ করে, আর বয়েস তো দেখতেই পাচ্ছেন। ঘরে একগাদা ছেলেপুলে, নিজের প্রথম পরিবার অনেক আগেই খতম হয়েছিল। ওর বড় জোয়ান ছেলেটাকেও মিলে ঢুকিয়ে তার বিয়ে দেবার চেষ্টায় এগিয়েছিল। কিন্তু ছেলের জন্য মেয়ে দেখতে গিয়ে নিজেরই মুণ্ডু ঘুরে গেল–চালাকি করে ও ব্যাটা নিজেই তাকে বিয়ে করে বসল। তারপর থেকেই বিষম ফ্যাসাদ। বাপে-ছেলেয় সাপ-বেজির সম্পর্ক, আর ওই ছেলের দিকেই বউটার গোপন টান।
…হবে না তো কি, বউটাকে তো আমি স্বচক্ষে দেখেছি–প্রথম দিন ওকে দূরে দাঁড় করিয়ে রেখে আমার সঙ্গে চুল কালো করার দরদস্তুর করতে এসেছিল। বড় ছেলেকে বাড়ি থেকে তাড়িয়েও বউকে বিশ্বাস করে না বলেই সঙ্গে এনেছিল নিশ্চয়। তখন দেখেছি। কালো পাথরে কোঁদা চেহারা–সর্বঅঙ্গে স্বাস্থ আর ইয়ে যেন চুঁইয়ে পড়েছে। এই বুড়ো অমন মেয়েমানুষ বশে রাখবে কী করে!
আমি নীরব শ্রোতা। একটু চুপ করে থেকে তেমনি খাটো গলায় অমল যেন প্রায় শ্লেষে কেটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে মারল। কিন্তু এবারে লিখলে বুড়োর বদলে আপনি ওই ছোঁড়াটাকে জেতাবেন কী করে–মা-ছেলে সম্পর্ক যে!
জবাব দিইনি। লেখারও বাসনা ছিল না।
কিন্তু তা হবার নয় বলেই বোধহয় দেড় মাস বাদে এই রঙ্গমঞ্চে আবার এক রাতে এই বুড়োর সঙ্গে দ্বিতীয় দফা দেখা। আরো ক্লিষ্ট আরো ঝড়ো মূর্তি। অমলের হাতে তার চুল কালো করার কাজ চার ভাগের তিন ভাগ শেষ।
অতএব ভোলা এসে আমার মাথা দখল করল। আর সেই দখল ছাড়ার মিনিটখানেক আগে ট্র্যাক থেকে সন্তর্পণে খুচরা পয়সা গুনে অমলের হাতে দিয়ে বুড়ো প্রস্থান করল।
আমি বাইরে এসে দেখি অদূরের লাইটপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে ফতুয়ার পকেট থেকে একটা ক্ষুদে আয়না বার করে বুড়োটা নিবিষ্টমনে তার কালো পালিশ-করা চর্চকে চুল পর্যবেক্ষণ করছে। ঘরের অত আলোতে দেখেও সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারেনি।
পাশ কাটাতে গিয়েও আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। গম্ভীর অথচ লঘু বিদ্রুপের সুরে বলে ফেললাম, চমৎকার হয়েছে, কেউ বুঝতে পারবে না।
অবাক চোখে লোকটা ঘুরে দাঁড়ালো, তারপরেই মুখে বোকা-বোকা হাসি।-হা হুজুর…তবে বড় খরচ।
হুজুর শুনে হোক বা খরচের কথায় বিমর্ষ শুকনো মুখ দেখে হোক, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নাম কী?
–আজ্ঞে কার্তিক দোলুই। এত কাছ থেকে মুখখানা যেন আরো ক্লিষ্ট বিমর্ষ লাগছে। আমার মনের অগোচরে কোনো খটকা লেগেছিল কিনা জানি না।–এখানে থাকো কোথায়?
–ফুটপাথে।
–আমি অবাক! আর কে থাকে?
–এখানে কেউ থাকে না হুজুর, বউ আর বাল-বাচ্চারা দেশে থাকে।
সত্যিই খটকা লাগছে।–দেশ কোথায়?
আমাকে সদয় ভেবেই লোকটার বিষণ্ণ মুখে কৃতজ্ঞতার আভাস।–মেদিনীপুর।
–তা অত খরচ করে পাকা চুল কালো করবার দরকার কী?
দুটো গর্তের করুণ দৃষ্টিটা আমার মুখের ওপর থমকালো।–কী করব, পেটের দায়–ভিক্ষে করতে মন সরে না।
-কেন? কী করো তুমি?
–আজ্ঞে হুজুর রিকশা টানি।…আমার সাদা চুল দেখে কেউ আমার রিকশায় উঠেতে চায় না, সব জোয়ানদের রিকশায় ওঠে।
কপালে হাত ঠেকিয়ে সেলাম করে লম্বা শ্রান্ত দেহটা টেনে টেনে লোকটা চলে যাচ্ছে। লাইটপোস্টের নাচে আমি হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে।
রমা মিত্র এবং মালবী মিত্র
…প্রশান্তকে তিনদিন বাদে আসতে বলেছিল মালবী মিত্র। বলেছিল তিনটে দিন সে ভয়ানক ব্যস্ত থাকবে, দু-দুটো ছবি শেষের মাথায়–সকালে রাত্রিতে দুদফা করে শুটিং, এর মধ্যে দুদণ্ড মাথা ঠাণ্ডা করে কিছু ভাবার সময় নেই। বলেছিল, দিনতিনেক পরে যেন সে আসে। তখন শুনবে। তখন ভাববে। তখন যা বলার বলবে। নিরুপায় ভূভঙ্গি করে হেসেই বলেছিল, এই দেখো না, এতকাল বাদে তোমাকে দেখে কী যে করব ভেবে পাচ্ছি না, অথচ দুটো ঘণ্টা তোমাকে বসিয়ে আদর-যত্ন করতে পারলাম না…কী যে জীবন আমাদের যদি জানতে!
প্রশান্ত জবাব না দিয়ে চুপচাপ মুখের দিকে চেয়েছিল। সেই পুরু দুটো কাঁচ, তার ওধারে সেই ডাগর দুটো চোখ, সেই রকমই একমাথা ঝাকড়া চুল। কে বলবে
এই মানুষ একটানা সাত বছর বিদেশের মাটি চষে, মস্ত মস্ত চাকরি করে কিছুদিন আগে দেশে ফিরেছে। মালবী এই মুখ আর এই চাউনি দেখে ভাবতে পারো বড় জোর সাত মাস দেখেনি মানুষটাকে।
চুপচাপ ওই রকম খানিক চেয়ে থেকে প্রশান্ত বলেছিল, আচ্ছা, তিন দিন পরেই আসব তাহলে। তক্ষুণি উঠে দাঁড়িয়েছিল।
হ্যাঁ, এসো, রাগ করলে না তো? ঠিক এসো কিন্তু
ট্রেনের রিজার্ভ কামরার পুরু গদীতে ঠেস দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে বসে আছে। মালবী। বাইরের গাঢ় অন্ধকারের পাতাল ছুঁড়ে ট্রেন ছুটেছে। ওটা আলোয় পৌঁছুবে। কিন্তু মালবী কোথায় ছুটেছে? সে অন্ধকার খুঁজছে। কোনো অস্তিত্বগ্রাসী অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাবার তাড়না তার। কিন্তু এমন জায়গা আছে কি…।
সামনের বার্থে অঘোরে ঘুমচ্ছে সারদা। ঝি ঠিক নয়, তার থেকে বয়সে বছর বারো বড় সহচরী বলা যেতে পারে, যে তার ঘর সামলায়। মনিবানীকে হঠাৎ এ ভাবে পড়িমরি করে বেরিয়ে পড়তে দেখে সে ততো অবাক হয়নি যত অবাক হয়েছে। টানা দুটো দিনের থমথমে মুখ দেখে। এত হাসি-খুশি যেন কোথায় উবে গেল! তারপর আজই হঠাৎ হুকুম, বেরুতে হবে। কোথায় যেতে হবে, কতদিনের মধ্যে যেতে হবে না জেনেই তড়িঘড়ি সব গোছগাছ করে নিতে হয়েছে। তা সহৃদয়া মনিবের এই গোছের খেয়ালের ধকল তাকে অনেক সামলাতে হয়। তাই আর থমথমে মুখের কারণ নিয়ে সে বিশেষ মাথা না গামিয়ে তোফা আরামে নিদ্রা দিয়েছে।
একবার তাকে দেখে নিয়ে অবসন্নের মত আবার বাইরের দিকে ফিরল মালবী মিত্র।
…সাত বছর বাদে প্রশান্ত এসেছিল কোনো একদিনের এক সাধারণ মেয়ে রমা মিত্রের কাছে। কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলেছে এক অসাধারণ মেয়ে মাধবী মিত্র। যার তুলনা নেই। যার দর্শন পেলে বহু রসিকজন ভাগ্য মানে। খ্যাতির বিড়ম্বনায় যে মালবী মিত্র সর্বসাধারণের নাগাল থেকে বিচ্ছিন্ন-মিনিট চল্লিশ সে মাধবী মিত্র কথা বলেছিল প্রশান্তর সঙ্গে। রমা মিত্র নয়…প্রশান্ত কি তা বুঝেছে? বুঝে গেছে? বোঝার কথা, কিন্তু মালবী সেই মুখের দিকে চেয়ে নিঃসংশয় হতে পারেনি। শুধু তাই নয়, কথা বার্তায়, বিস্ময় আর হাসি-খুশির ফাঁকে মালবী তাকে প্রকারান্তরে এও বোঝাতে চেষ্টা করেছে, সাত বছর বাদে লোকটা এসে যে-কথা বলছে তার মধ্যে অবিশ্বাস অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। কিন্তু লোকটা এও বুঝেছে কিনা সন্দেহ…রমা মিত্র নয়, আপন। মহিমায় বিকশিত এক মালবী মিত্র তাকে বলেছে আপাতত দিন-তিনেক তার মরবার ফুরসত নেই, তিন দিন পরে যেন আসে। প্রশান্ত বলেছে তাই আসবে।
..এই রাতটা পোহালে তিনটে দিনের অবসান। কালই বিকেলের দিকে প্রশান্ত আবার আসবে। ঢোকবার সময় বাড়ির দরজা-জানলা বন্ধ দেখে একটু অবাক হবে। তারপর দরজায় তালা ঝুলছে দেখে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে থাকবে।…
মালবীর ঠোঁটের ডগায় কৌতুকের মত রেখা পড়ল একটু। কিন্তু চোখ দুটো অস্বাভাবিক চকচক করছে। বিগত এই কটা বছর শিল্পের তাগিদে ঠোঁটে তার অজস্র কৌতুক ঝরেছে, আর চোখ তার অজস্রবার চকচকিয়ে উঠে দুগাল বেয়ে ধারা নামিয়েছে। কিন্তু এর সঙ্গে সে-সবের মিল নেই।
রমা নিত্ৰ এখনো ভস্মস্তূপে পরিণত হয়নি। আর সেই ভস্মস্তূপ থেকে তখন। কোনো মালবী মিত্রর আবির্ভাব ঘটেনি।
এম. এ. পড়া একটি অতি সাধারণ মেয়ে রমা মিত্র। মামুলি প্রেমে পড়েছিল একটি বনেদী ঘরের সাধারণ ছেলের সঙ্গেই যার নাম প্রশান্ত ঘোষ। কিন্তু রমা মিত্র প্রায় অসাধারণই ভাবত তাকে। ভাবতে ভালো লাগত।
রমা রূপসী কিছু নয় যে নিজের সম্পর্কে বাড়তি গর্ব পুষবে। গায়ের রং বলতে গেলে কালোই। স্বাস্থ্যটা ভালো এই যা। আর যাদের দরদ আছে তারা নাক মুখ চোখও ভালো দেখে। তবে ফটো ওর খুব সুন্দর ওঠে, সত্যিকারের চেহারা থেকে ঢের বেশি সুন্দর মনে হয়। ফটোতে তো আর গায়ের রঙ ধরা পড়ে না। বি.এ. পাস করার পরেই তার বাবা এক বড় ঘরে মেয়ে দেবার আশায় ওর একখানা ছবি পাঠিয়েছিল পাত্রপক্ষের কাছে। ছবি দেখেই পাত্রপক্ষ সাগ্রহে এগিয়ে এসেছিল মেয়ে দেখতে। কিন্তু রঙ দেখে ফিরে গেছে। মোটামুটি ফর্সা হলেও হয়ত আটকাতো না, কিন্তু রমাকে ঠিক মোটামুটি ফর্সাও কেউ বলবে না।
কিন্তু গর্ব করার কত রমার গুণও একটু ছিল। খুব সুন্দর থিয়েটার করত স্কুল আর কলেজে পড়তে। মেয়ে-কলেজের সেই থিয়েটার দেখে অনেক ছেলে অনেক রূপসী মেয়ের থেকেও তার দিকে বেশি ঝুঁকত। ওর বাবা কোন ফার্মের বাঁধা মাইনের কমার্সিয়াল আর্টিস্ট হলেও আর্টিস্ট তো বটেন। উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। মেয়ের এই সখে বাধা দেননি কখনো। এম.এ. পড়ার সময়ও কি এক ব্যাপারে পাড়ার মেয়েরা মিলে থিয়েটার করেছিল। রমা মিত্র তার নায়িকা এবং সর্বাধিনায়িকা। সেই যশের দুদুটো অ্যামেচার থিয়েটার দলের ভদ্রলোকেরা ওর বাবাকে পর্যন্ত ধরে পড়েছিল, মেয়েকে থিয়েটার করতে দিতে হবে। নিরুপায় ভালমানুষ বাবা মেয়ের কাছেই পাঠিয়ে ছিলেন তাদের। রমা তাদের তাড়িয়েছে।
যাক, ওটা জীবনের ক্ষেত্র নয়–অন্য সব ক্ষেত্রেই রমা মিত্র নিজেকে অতি সাধারণের উর্ধ্বে ভাবত না কখনো। আর তার এই মাধুর্যটুকুই কারো কারো চোখে পড়ত, মনেও বোধহয় ধরত। বিশেষ করে চোখে পড়েছিল আর মনে ধরেছিল প্রশান্তর।
এই প্রেমে পড়া এমন কি তার পরিণতিও অনেকটা ছকে বাঁধা মামুলি ব্যাপার। হাজারগণ্ডা ছেলে-মেয়ে হামেশাই এ-রকম প্রেমে পড়ে থাকে। মিলন অথবা বিচ্ছেদের পরিণামে সচরাচর সে-রকম কিছু বৈচিত্র্যও চোখে পড়ে না। কিন্তু যে ছেলেটা আর যে মেয়েটা সেই মামুলি প্রেমে পড়ে, তাদের চোখে এখন দুনিয়ার রঙ আলাদা।
রমা যখন বিয়ে পড়ে তখন পরিচয়। পরিচয়ের রাস্তাটাও চিরাচরিত এবং সাজানো। রমার সহপাঠিনী সুমিতার মাসতুতো দাদা প্রশান্ত। সেখানেই দেখা-সাক্ষাৎ এবং আলাপ। প্রশান্ত তখন এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ে। অবকাশ কম। কিন্তু ছুটিছাটায় বাড়ি এলে প্রায়ই তাকে সুমিতার ওখানে দেখা যায়। একদিন সুমিতাই প্রশান্তর মাসির বাড়ি আসার টানের কারণটা রমার কাছে ফাঁস করে দিল। বলল, প্রশান্তদা কলকাতায় এলেই ঘন ঘন আমাদের বাড়ি আসে কেন জানিস? তোর জন্য। তোকে ভালো লাগে।
সেই প্রথম রমা দুচোখ বড় বড় করে শুনল একটা ছেলের তাকে ভালো লাগে, আর সেই জন্যে সে তার মাসির বাড়ি আসে। ভালো লাগার কারণটাই খুব বিচিত্র লাগল তার। মেয়ে কলেজের চিত্রাঙ্গদা নাটক দেখার পর থেকেই নাকি এই ভালো। লাগার সূত্রপাত। রমা যখন চিত্রাঙ্গদা করেছিল তখন ফার্স্ট ইয়ার ছাড়িয়ে সবে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠেছে। তখন নাচতেও পারত ভালো। চিত্রাঙ্গদা করে দুই একটা মেডেল টেডেল পেয়েছিল বটে, কিন্তু কোন ছেলের মনে এই গোছের ছাপ ফেলতে পেরেছে। সেটা কল্পনাও করেনি।
এর পর থেকে বলা বাহুল্য সুমিতার প্রশান্তদাকে সে একটু বিশেষ দৃষ্টিতেই দেখতে লাগল। পড়াশুনায় রমা সাদামাটা ছাত্রী, কিন্তু সুমিতার প্রশান্তদা শুনল স্কলারশিপ পাওয়া ছেলে। এনজিনিয়ারিং-এও প্রতি বছর ফার্স্ট হচ্ছে। রমার মনে তাইতে সঙ্কোচ একটু। কিন্তু পুরু কঁচের ওধারে প্রশান্তর চোখ দুটো যখন ঘুরে ফিরে তার দিকেই আটকে থাকত আর ঠোঁটের ফাঁকে একটু দুষ্টু-দুষ্টু হাসি লেগে থাকত। রমার তখন ছেলেমানুষই লাগত তাকে।
রমা যেবার বি.এ. পাস করল, প্রশান্ত সেবার এনজিনিয়ারিং পাস করে বেরুল। পাস করার সঙ্গে সঙ্গে ভালো মাইনের চাকরি। একে কৃতী ছেলে, তায় মুরুব্বির জোর আছে। তার বড়দাও আধা-প্রবীণ এনজিনিয়ার–বম্বের এক নামজাদা ডিজাইন অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন ফার্মে মস্ত চাকরি করে। তার সুপারিশে তাদের কলকাতার শাখায়। বহাল হয়ে গেল সে। প্রশান্ত খুঁতখুঁত করেও বাপের হুকুম অমান্য করতে পারল না। তার ভয়ানক ইচ্ছে ছিল বিলেতে গিয়ে আরো কিছু ডিগ্রি-টিগ্রি পকেটস্থ হবার পর কর্মজীবন শুরু করে। কিন্তু বাপের ইচ্ছেটাই তাদের পরিবারে সব! তার বাবা জবরদস্ত পুলিস-অফিসার ছিলেন। অনেককাল রিটায়ার করেছেন। কিন্তু পারিবারিক ক্ষেত্রে ভদ্রলোকের পুলিসী মেজাজ এখনো অক্ষুণ্ণ আছে। সেই বাপ হুকুম করল–দাদা যা ব্যবস্থা করেছে তাই করো, চাকরিতে ঢোকো।
ছেলে মুখ সেলাই করে চাকরিতে ঢুকেছে।
প্রেমে হাবুডুবু অবস্থা নয় তাদের তখনো। আলাপ বেশ ঘনীভূত হয়েছে এই পর্যন্ত। আর তার ফলে প্রশান্তকে ভালো লাগতে শুরু করেছে এই পর্যন্ত। কিন্তু সুমিতার মুখে তাদের বনেদী বাড়ির কর্তাটির দাপটের কথা যা শোনে তাতে রমার ভয়ই করে। তবু সেই ভদ্রলোক ছেলের বিলেত যাওয়া বন্ধ করল বলে মনে মনে খুশিই হল। নিজের মনেই বলেছে, বেশ হয়েছে, বিলেত গিয়ে ছেলে একেবারে লাটসাহেব বনে আসবে!
প্রেমে হাবুডুবু অবস্থাটা দাঁড়াল রমার এম-এ পড়ার দুটি বছরে। প্রায়ই আপিস পালিয়ে প্রশান্ত ছেলেমানুষের মতই য়ুনিভার্সিটির দোরগোড়ায় ওর ছুটির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। গোড়ায় গোড়ায় রমা লজ্জা পেত। ক্লাসসুদ্ধ ছেলে-মেয়ে জেনে ফেলেছে। কিন্তু শেষে এটা সহজ হয়ে গেল। গল্প করতে করতে দুজনে এসপ্লানেড পর্যন্ত হাঁটে। রেস্টুরেন্টে খায়। তারপর ট্রামে পাশাপাশি বসে সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফেরে। প্রশান্তর বাড়িতে জানে ছেলের কাজের চাপ, রমার বাড়িতে জানে মেয়ের লাইব্রেরিতে পড়ার চাপ। য়ুনিভার্সিটি আর আপিস পালিয়ে দুজনে সিনেমাও দেখে মাঝে মাঝে।
রমা বলে, তোমার জন্যে আমি ঠিক ফেল করব, তখন লজ্জায় আর মুখ দেখাতে পারব না।
প্রশান্ত জবাব দেয়, হু, ভারী তো বাংলা পড়া তার আবার ফেল!
রাগ দেখাতে গিয়েও কী মনে পড়তে রমা হেসে ফেলে, কী বললে, ভারী তো বাংলা–বলতে লজ্জা করে না, বাংলায় একটা চিঠি লিখতে সাতটা বানান ভুল হয়, বই পড়ার সঙ্গে শাড়ি পরার বানানের তফাৎ জানে না!
সেদিন সিনেমা দেখার প্রোগ্রাম করে প্রশান্ত রমাকে চিঠি লিখেছিল, ওমুক-রঙা শাড়িখানা পরে যেন আসে। তাইতেই বানানের বিভ্রাট।
কিন্তু প্রেম-প্রীতির ব্যাপারটা জানাজানি হতে আর বেশি দেরি হল না। প্রশান্তর বাবা সঠিক হদিস পেলেন সুমিতাকে জেরা করে। কার মেয়ে কেমন মেয়ে জানার পর ছেলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ তিনি। ওদিকে প্রশান্তর এক দাদার বিয়ে তখনো বাকি, সে সাধারণ চাকরি করে। তার বিয়েটা দিয়ে ফেলে কৃতী এনজিনিয়ার ছেলের জন্য অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা আনার সঙ্কল্প। বড় বড় ঘর থেকে প্রস্তাব আসছেও। তার মধ্যে এ-রকম ছেলেমানুষি বরদাস্ত করার মত নরম মন নয় তার। তাই ছেলেকে ডেকে বেশ কড়া সুরেই হুমকি দিলেন, বাপু হে, তোমার ছোড়দার বিয়েটা হয়ে গেলে তোমার। বিয়ে আমিই দেব। ততদিন ঠাণ্ডা মাথায় কাজের উন্নতি যাতে হয় সেই চেষ্টা করো।
বাবার হুমকির খবরটা সেদিনই রমাকে দিল সে। এই গুণটা আছে। নিজের সমস্যাটা দুজনের সমস্যা ভাবে। তাই সব কথাই রমাকে বলে। শোনামাত্র দুচোখ কপালে–সর্বনাশ! তাহলে?
ঠোঁট উল্টে প্রশান্ত জবাব দিল, সর্বনাশ আবার কি, ও-সব পুলিশী দাপটে দেশের স্বাধীনতা ঠেকানো গেছে?
রমা বলল, দুটো এক হল! তাতেও তো কত লোকে জীবন দিয়েছে।
আমিও তো একজনকে আমার জীবন দিয়েছি।
কী ভালো যে লেগেছিল শুনতে রমাই জানে। সেদিন সন্ধ্যার আড়ালে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কোণের চত্বরে বসে দুজনে যত কাছাকাছি হয়েছিল এর আগে ততটা আর কখনো হয়নি। সেদিন রাতে ভালো ঘুমুতে পারেনি রমা। দুটো ঠোঁটের সেই ঘন আবেগের স্পর্শ সমস্ত রাত ধরে তার সর্বাঙ্গে আবেশ ছড়িয়েছে আর বিহ্বল করেছে।
এমন অদ্ভুত ছেলেমানুষি প্রস্তাবও করে মানুষটা যে রমা হেসে বাঁচে না। সেদিন। ওর বাবার হুমকির প্রসঙ্গেই রমা বলেছিল, কিন্তু আমার বাপু সত্যি কেমন ভয় করছে!
প্রশান্ত তক্ষুনি বলেছিল, আমারও করছে।
তাহলে?
তাহলে চলো পালাই দুজনে। কিন্তু বাবা যা লোক, ঠিক আবার ধরে আনবে।
তাহলে?
তাহলে আর এক কাজ করা যাক। চলো কোন সাধু-সন্ন্যাসীর কাছে যাই, মন্ত্রের জোরে তারা বাবার মন বদলে দিক।
রমা হেসে উঠেছিল। তারপর বলেছিল, বিয়েটা হয়ে গেলে মন আমিই বদলে দিতে পারি বোধহয়।
প্রশান্ত সাগ্রহে বলে উঠেছিল, তাহলে তাই করে ফেলি এসো। রেজিষ্ট্রি বিয়ে করে সোজা বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াই।
ও বাবা! রমা আঁতকেই উঠেছিল, তোমার বাবার সামনে?
এরকম উদ্ভট উদ্ভট অনেক প্রস্তাব করে সে। কখনো বলে বাড়ি গিয়ে মাকে শাসাবে, এ বিয়ে না দিলে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়বে। কখনো ভাবে মাকে শেখাবে, এ বিয়ের জন্য ইষ্টদেবার স্বপ্ন-টপ্ন দেখেছে সেই গোছের কিছু ভাঁওতা দিয়ে বাবাকে বশ করতে।…সেদিন তো এমন মোক্ষম প্ল্যান মাথায় গজালো তার যে আপিস ফেলে রমাদের বাড়িতে এসে হাজির। রমার য়ুনিভার্সিটি ছুটি সেদিন। চুপি চুপি তাকে বাইরে টেনে আনল। সাগ্রহে বলল, তোমার সাহসে কুলোলে এবার আর কেউ আটকাতে পারবে না–পারবে?
সত্যি তেমন কিছু আশা করেছিল রমা। কী করতে হবে?
দু তিনদিনের মধ্যেই দুজনে পালাব আমরা।
এ তো পুরনো প্রান!
আঃ! আগে শুনোই না, তার কয়েকদিনের মধ্যে কাগজে চিঠি পাঠাব আমরা মানে ওমুক মেয়ে আর ছেলে একসঙ্গে আত্মহত্যা করেছে, ব্যস!
রমার দুচোখ বিস্ফারিত। কী ব্যস, কাগজে খবর পাঠিয়ে আমরা আত্মহত্যা করব?
দূর পাগল, আমরা বিয়ে করব–সকলে জানবে আমরা আত্মহত্যা করেছি!
আস্ত পাগল তুমি! আচ্ছা স্কলারশিপ পেলে কী করে? অত ভালো এনজিনিয়ারিং পাসই বা করলে কী করে?
কেন?
— উড়ো খবর কাগজে ছাপবে কেন?
দুজনে একসঙ্গে ছবি তুলে কাগজে পাঠিয়ে দেব বাইরে থেকে–এই দুজন আত্মহত্যা করেছে–অন্য লোক খবর পাঠিয়েছে।
আত্মহত্যা করলে আমাদের বডি যাবে কোথায়? পুলিস চুপ করে বসে থাকবে? আমাদের টেনে বার করবে না? তখন আত্মহত্যাই করতে হবে!
এমন প্ল্যানটাও বাতিল হয়ে যেতে প্রশান্ত বিমর্ষ। রমা না থাকলে সে যে এতদিন একটা কিছু চমকপ্রদ বিভ্রাট বাঁধিয়ে বসত তাতে সন্দেহ নেই।
রমা এম.এ. পাশ করার পর দুজনেই অনেকখানি বেপরোয়া হয়ে উঠল। ওদিকে প্রশান্তর ছোড়দার বিয়ে হয়ে গেছে। তার বাবা তখন কৃতী ছেলের বিয়ের তোড়জোড় করছেন। প্রশান্ত স্পষ্টই তার মাকে জানিয়ে দিয়েছে বিয়ে কোথায় করবে। তার ফলে বাপ আগুন, মাও অসন্তুষ্ট। বাড়িতে অশান্তি। বাবাও ঘোষণা করেছেন, অবাধ্য হলে ছেলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না।
রমা এম.এ. পাস করার পর প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করল, এবার?
রমা জবাব দিল, এবারে চাকরি।
কী চাকরি? কোথায় চাকরি?
স্কুলে স্কুলে-মাস্টারি ছাড়া আমি কী আর পেতে পারি?
খবরদার!
বা রে, তাহলে কি করব? বাবা আর কতকাল টানবেন?
খপ করে তাকে কাছে টেনে প্রশান্ত বলেছে, বাবা কেন, আমি টানব।
রমা হেসে ফেলেও ভ্রূকুটি করেছে–বিয়ের আগেই?
প্রশান্ত ভেবে-চিন্তে বলেছে, না, চোখ-কান বুজে এবারে বিয়েটাই আগে করে ফেলা যাক। কী আর হবে, বাপ মেরে ফেলতে তো আর পারবে না, বড়জোর আলাদা করে দেবে।
কিন্তু রমার মনে সায় দেয় না। কারণ অভিশাপ দিয়ে ঘর বাঁধবো কেমন করে?
ছুটির দিনে বেশ সকাল সকাল এক এক দিকে বেরিয়ে পড়ে দুজনে। কখনো ব্যাণ্ডেল, কখনো কাঁচড়াপাড়া, কখনো বা গঙ্গার বুকে ডিঙি নৌকায়। আর সমস্যার সমাধান কেমন করে হবে তাই ভাবে দুজনে। বিশেষ করে নির্জন বন-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে দুজনেরই। সেই নির্জনতার একটা ভাষা আছে। হাত ধরা ধরি করে শুকনো পাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে এগোয় দুজনে। গাছের ছায়ায় ঘন হয়ে বসে। দুপুরে পাখির অলস ডাক কান পেতে শোনে। সমস্যা-টমস্যা সব দুজনেরই ভুল হয়ে যায় তখন।
রমা একদিন ঝগড়া টেনে আনে।-তুমি আমাকে ভালোবাস না ছাই, আসলে চিত্রাঙ্গদা পছন্দ তোমার!
তুমি তো চিত্রাঙ্গদা।
আমি রমা। তবে চিত্রাঙ্গদার মত কুৎসিত বটে
চিত্রাঙ্গদা কুৎসিত?
না তো কি?
তাহলে তুমি একটি অন্ধ, ভেতর দেখতে জানো না।
কথাগুলো যেন কান পেতে আস্বাদন করার মত। রমার অনেকদিন মনে হয়েছে লোকটা এনজিনিয়ার বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কবি। শুধু কবি নয়, একেবারে অবুঝ কবি।
সামনের গাছটার দিকে তাকিয়ে কাব্যই করল প্রশান্ত। বলল, আমি যদি গাছ। হতাম, আর তুমি ওই লতার মত আমার সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে, বেশ হত।
রমা তক্ষুনি তার কাঁধে গা ঠেকিয়ে আর একটা হাতে তার গলা বেষ্টন করে বলল, লতা হবার দরকার কী, এই তো জড়িয়ে থাকলাম।
সেদিন ওই ঠাণ্ডা মানুষটার রক্তে কেন যে অত দোল লাগল রমা জানে না। এরকম তো আগেও হয়েছে। আগেও কাছে টেনে নিয়েছে। দুই উষ্ণ ঠোঁটের আবেগ ওর অধরের বাধা বিচূর্ণ করেছে। কিন্তু এই দিনের তৃষ্ণার মূর্তিটাই অন্যরকম। ওর দেহটা যেন ক্রমে একটা আবিষ্কারের বস্তু হয়ে উঠতে লাগল। নিবিড় নিষ্পেষণে সর্বাঙ্গে কী রকম একটা যন্ত্রণার শিহরণ, রমা যেন কোথা থেকে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে!
হঠাৎ ওকে দুহাতে ঠেলে দিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল সে। বিস্রস্ত বসন ঠিক করতে করতে ধমকের সুরে বলে উঠল, এই!
একটা ভুত নামল যেন প্রশান্তর কাঁধ থেকে। আত্মস্থ, বিব্রত।–কি?
রাক্ষুসেপনা কোরো না, সময় ফুরিয়ে গেল নাকি!
.
কিন্তু শিগগীরিই একটা ধাক্কা খেয়ে দুজনেরই মনে হল সময় ফুরিয়ে গেল বুঝি। প্রশান্তর সঙ্গে তার বাবার মুখোমুখি একটা সংঘাত হয়ে গেল এক বড়লোকের বাড়ির মেয়ে দেখতে যাওয়া নিয়ে। খুব বিনীত আর খুব স্পষ্ট ভাবে প্রশান্ত এবার বাবাকেই জবাব দিয়েছে, তার দেখতে যাওয়া সম্ভব নয়, এবং কারোরই না যাওয়া ভাল।
প্রাথমিক ঝড়টা প্রশান্তর উপর দিয়ে গেল। তারপর ভেবেচিন্তে ভদ্রলোক রমার বাবাকে ডেকে পাঠালেন একদিন। রমার বাবা এলেন।
প্রশান্তর বাবা রূঢ়মুখে জানতে চাইলেন, মেয়ের বিয়েতে তিনি কী করতে পারবেন?
রমার বাপ জবাব দিলেন, আপনি চাইলে শুধু বিয়েই দিতে পারব, আর কিছু করার সঙ্গতি নেই।
তপ্ত বক্রস্বরে প্রশান্তর বাবা বললেন, সেটা কি বেশী আশা করা হচ্ছে না?
রমার বাবা জবাব দিলেন, এর মধ্যে আমার কোন হাত নেই।
আপনার মেয়েকে বোঝাবার হাত বা দায় আমার?
আপনার ছেলেকে বোঝাবার হাত বা দায় আপনার।
নিঃস্ব লোকের এই উক্তিতে প্রশান্তর বাবা অপমানিত বোধ করলেন। আর আসল অপমানিত মানুষটি নিঃশব্দে উঠে গেলেন।
সব শুনে রমা রাগে জ্বলতে লাগল। বাবা ওর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নিয়ে ও-বাড়ি থেকে ফেরেননি। তবু বাবার অপমান ওকে মর্মান্তিকভাবে বিধল। ঘরে মা নেই-ভাইবোনদের কাছে বাবা অনেকখানি।
ওদিকে এ ঘটনার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই প্রশান্তর বাবা তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। ছেলেকে কলকাতা থেকে আপাতত সরাতে না পারলে এ মোহ কাটবে না, তাই বোম্বেতে বড় ছেলের সঙ্গে এ নিয়ে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান চলছিল। রমার বাবার সঙ্গে কথা হবার পনের দিনের মধ্যে হেড-অফিস অর্থাৎ বম্বেতে পত্রপাঠ। বদলির অর্ডার পেল প্রশান্ত। সেটা যে দাদারই চেষ্টার ফল, বুঝতে কারো বাকি থাকল না।
এ খবরও রমা শুনল প্রশান্তর মুখ থেকেই। শোনার পর গুম সে। একটু বাদে বিরস মুখে জিজ্ঞাসা করল, বম্বে যাচ্ছ?
তুমি কী বলো, চাকরি ছেড়ে দেব?
আবার একটু চুপ করে থেকে রমা বলল, না, যাও।
প্রশান্ত অসহিষ্ণু, উতলাও।
তুমি এভাবে কথা বলছ কেন? সব তো জানো, আমার কী দোষ? তাছাড়া এই করে বাবা বা দাদা বা দুনিয়ার কেউ আমাদের আটকাতে পারবে?
পারবে না?
পাগল! এক বছরে হোক, দু বছরে হোক, পাঁচ বছরে হোক–বিয়ে আমাদের হবেই। যতদিন না হয়, আমার প্রতীক্ষায় তুমি থাকবে, তোমার প্রতীক্ষায় আমি থাকব।
সত্যি?
সত্যি।
সত্যি?
সত্যি সত্যি সত্যি। মুখের দিকে চেয়ে থেকে প্রশান্ত বিষণ্ণ মুখে হাসল একটু, কিন্তু আমাকে এখনো তুমি বিশ্বাস করলে না!
বিশ্বাস করলাম না?
প্রশান্ত মাথা নাড়ল, না।
দরদে রমার ভিতরটা ভরে গেল। দুহাত বাড়িয়ে তার মাথাটা বুকে টেনে আনল। বলল, বিশ্বাস করেছি। তুমি আমার অপেক্ষায় থাকবে, আমিও তোমার প্রতীক্ষায় থাকব।
তিন দিনের মধ্যে প্রশান্ত বম্বে চলে গেল। আর তিন মাসের মধ্যে তার চিঠি পেল লণ্ডনগামী জাহাজ থেকে। সুযোগ পেয়ে চাকরি ছেড়ে সে সাগর পাড়ি দিচ্ছে! রমা যেন প্রতীক্ষায় থাকে।
এই সবই ঘটে গেল রমা এম. এ. পাশ করার ছমাসের মধ্যে।
আর আরো দুমাস বাদে রমার মাথায় বুঝি বাজ পড়ল একটা। খবরটা দিল সুমিতা। তার অনেকদিন বিয়ে হয়ে গেছে। হঠাৎ দেখা। কথায় কথায় বলল, বিলেত গিয়ে প্রশান্তদা মেম বিয়ে করেছে, শুনেছিস?
রমা চমকে উঠল। তারপর অবিশ্বাস করল। বিশ্বাস করবে কী করে–মাত্র তিন সপ্তাহ আগেও সে প্রশান্তর আবেগভরা চিঠি পেয়েছে। তার এত অবিশ্বাস দেখেই পরে সুমিতা মাসির বাড়ি গিয়ে একখানা ছবি আর মাকে লেখা প্রশান্তর নিজের হাতে লেখা চিঠি নিয়ে এলো। তাদের বাড়িতে নাকি হুলুস্থুল ব্যাপার চলেছে সেই থেকে।
অবিশ্বাসের আর কিছু নেই। এক তরুণী শ্বেতাঙ্গিনীর বাহু বেষ্টন করে প্রশান্ত দাঁড়িয়ে। দুখানি হাস্যোজ্জ্বল মুখ। চিঠিতে লিখেছে, তোমরা আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না জানি, পারো তো আমাদের আশীর্বাদ করো।
এরপর দিনকয়েক পর্যন্ত রমার মাথায় শুধু আগুন জ্বলেছে।
এদিকে রমার বাবাও কিছু ঝামেলার মধ্যে ছিলেন, বাড়ি ছাড়ার কেস চলছিল বাড়িঅলার সঙ্গে। প্রতিপক্ষ ডিক্রি পেয়েছে, তিনমাসের মধ্যে বাড়ি ছাড়ার হুকুম হয়েছে। তার মধ্যে মেয়ের এই আঘাত। একমাসের ছুটির দরখাস্ত করে ভদ্রলোক ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। আর তারপর ফিরে এসে অন্যত্র উঠলেন।
ভিতরে ভিতরে যাতনার মত একটা তাগিদ অনুভব করত রমা। সাধারণ মেয়ের অসামান্য হয়ে ওঠার তাগিদ। ভিতরটা যেন একটা জ্বলন্ত অঙ্গার হয়ে উঠছে তার, আর এই তাগিদ বাড়ছে।
আগে স্কুল-মাস্টারির চেষ্টা করছিল, এখন সে চেষ্টা ছেড়ে দিল।
এই অবস্থার মধ্যে হঠাৎ এক নামজাদা চিত্রপরিচালকের নামে বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল একটা। নায়িকার ভূমিকার জন্যে একজন শিক্ষিতা অভিনেত্রী চাই। ফোটোসহ আবেদন করতে হবে।
মাথায় একটা ঝোঁকই চাপল রমার। নতুন করে নিজের ছবি তুলিয়ে আবেদন। পাঠিয়ে দিল।
অসামান্য হবার যোগ্যতা ছিল রমা মিত্রের। ডাক এসেছে। কথা বলে আর ছাত্রজীবনের অভিনয়ের মেডেল দেখে পরিচালক খুশি একটু। ট্রায়েল দিয়ে আরো খুশি। চমৎকার ফোটোজনিক মুখ, সুন্দর বয়েস, নাক মুখ চোখ ভালো–তার ওপর অভিনয়ে বুদ্ধিদৃপ্ত সহজ দক্ষতা আছে। আশাতীত পছন্দ হল তার।
.
রমা মিত্র মরে গেল। ছবিতে এক মালবী মিত্রের আবির্ভাব দেখল সকলে। প্রথম। ছবিতে এমন বিপুল বন্দনা কম নায়িকার ভাগ্যেই জুটেছে।
তারপর এই দুবছরে দিনে দিনে তার আবির্ভাব স্থায়ী হয়েছে, উজ্জ্বলতর হয়েছে। আজ মালবী মিত্র একটা নাম। সে অসামান্যা। তার নিঃশ্বাস ফেলার ফুরসৎ নেই।
কটা ছবির কাজ একসঙ্গে শেষ হতে মালবী একটু হাঁপ ফেলেছিল। নতুন কোন কোন ছবি হাতে নেওয়া যেতে পারে ভাবছিল। ধরছে তো এসে কতজনই। বম্বে থেকে ডাক এসেছে, তাতেও সাড়া দেবে কিনা চিন্তা করতে হবে।
এমন দিনে প্রশান্ত ঘোষ এসে হাজির। সারদার হাতে চিরকুট দেখেও নির্বাক খানিক। সেই পুরনো জ্বালা আর অনুভূতিটা নতুন করে আবার মাথার দিকে উঠছে। প্রথমে ভাবল সারদাকে বলে দেয়, দেখা হবে না বলগে যা। কিন্তু তা বলল না। বলল, এখানে নিয়ে আয়।
নিয়ে এলো। সেই মুখ, সেই পুরু কাঁচের চশমা, ঠোঁটের ডগায় সেই কাঁচা হাসি। দেখামাত্র রাগে সর্বাঙ্গ চিনচিন করে উঠল ভেতরটা।
প্রশান্ত দুচোখ ভরে দেখল তাকে খানিক।-কেমন আছ রমা?
রমা আবার কে, আমি তো মালবী! মালবী মিত্র!
প্রশান্ত হেসে উঠল, কি ফ্যাসাদেই যে ফেলেছিল এই নাম নিয়ে–যাকে সকলে চেনে তাকে কেউ চেনে না! বাইরে থেকে ফিরে এই একটা মাস হন্যে হয়ে খুঁজেছি তোমাকে। শেষে সুমিতার কাছে শুনলাম তুমি এখন উজ্জ্বলতম তারকা মালবী মিত্র। ..বিলেত থেকেও তোমাকে কত যে চিঠি লিখেছি, জবাব না পেয়ে শেষে হাল ছেড়েছি।
…বাড়ি ছেড়েছিল তাই চিঠি পায়নি৷৷ পেলেও জবাব দিত না। চোখে চোখ রেখে মালবী চেয়ে আছে।একা ফিরেছ না মেম-বউকেও এনেছ?
প্রশান্ত অবাক।–মেমবউ!
ভিতরটা দাউ দাউ করে জ্বলছে এখন। এমন নির্লজ্জও মানুষ হয়! ঠাণ্ডা গলায় বলল, তোমাদের কাঁধে হাত রাখা যুগল ছবি আমি দেখেছি, আর তোমার মাকে লেখা তোমার সেই চিঠিও আমি পড়েছি।
প্রশান্তর দুচোখ বিস্ফারিত প্রথম। তারপরেই হা-হা হাসি।–সে-সব তুমিও কি বিশ্বাস করেছ নাকি? কি আশ্চর্য! আমার প্রত্যেকবারের প্ল্যান তুমি বাতিল করেছিলে–তাই বিলেতে গিয়েই বাবাকে জব্দ করার মোক্ষম প্ল্যান ফেঁদেছিলাম। বাবার ওপর আমার তখন দুনিয়ার সব থেকে বেশি রাগ–আর কাঁধে হাত রেখে ছবি তোলার মত অন্তরঙ্গতা ও-দেশে একটু চেষ্টা করলেই হয়।
মুহূর্তের মধ্যে এ কি হল মালবীর? মাথাটা এমন প্রচণ্ডভাবে ঝিমঝিম করে উঠল কেন? তার অস্তিত্ব সুদ্ধ এভাবে নড়েচড়ে উঠল কেন? প্রাণপণে এই কথাগুলো ভণ্ডামী ভাবতে চেষ্টা করল কেন? আর ঘরে এত আলো, অথচ সামনে রাজ্যের অন্ধকার ভিড় করে আসছে কেন?
প্রশান্তও বিস্মিত চোখে চেয়ে আছে তার দিকে।
প্রাণপণ চেষ্টায় মালবী সামলে নিল নিজেকে।–বিশ্বাস করতে বলছ?
কী আশ্চর্য, আমি বলছি তাও বিশ্বাস করবে না?
মালবী দেখছে তাকে। অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে।–তারপর?
তারপর আবার কি, এবারে বিয়ে। বাবা তো আর নেই, আর মায়ের যা অবস্থা, তোমাকে ঘরে আনতে পারলে বাঁচেন।
বসার চেয়ারটা, মাটি, বাড়িঘর যেন দুলছে মালবীর চোখের সামনে। তবু হাসি মুখেই বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু আমি যে অভিনেত্রী হয়েছি!
মাথা ঝাঁকিয়ে প্রশান্ত বলল, কথা যদি রেখে থাকো, মানে আমার জন্যে প্রতীক্ষা যদি করে থাকো, তাহলে আর কোন কিছুতে যায় আসে না।
চেয়ার মাটি ঘর দুয়ার আর একবার বিষম দুলে উঠেছে। তারপর মালবী হেসেছে। নিজের জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট মনে পড়েছে। কাজের চাপে আপাতত মরবার ফুরসৎ নেই বলেছে। বলেছে, মাথায় কোনো কথা ঢুকছেই না এখন। তিন দিন বাদে তাকে আসতে বলেছে। তখন কথা হবে।
কিছু একটা ব্যতিক্রম অনুভব করেই প্রশান্ত লক্ষ্য করেছে তাকে। তারপর তিনদিন বাদে আসবে জানিয়ে উঠে চলে গেছে।
তিনদিনের মধ্যে দুরাত এক মিনিটের জন্যেও মালবী ঘুমোয়নি। আজ তার পালাবার তাগিদ।
কারণ সে তার মন দিয়ে বুঝেছে, প্রশান্ত এক বর্ণও মিথ্যে বলেনি।
তার কারণ, মালবী তার জন্য প্রতীক্ষা করেনি।…অসামান্য হয়ে ওঠার দুর্বার তাগিদে তার যৌবন-বাস্তবে একাধিক পুরুষের অভ্যর্থনা ঘটে গেছে। মালবী এতটুকু পরোয়া করেনি।
অন্ধকার বিদীর্ণ করে ট্রেন ছুটেছে। আলোয় পৌঁছুবে। কিন্তু মালবী ছুটেছে তেমনি অন্ধকারে নিজেকে মিলিয়ে দেবার তাড়নায়।
রমা মিত্রর ভস্ম থেকে একদিন মালবী মিত্র উঠে এসেছিল। আজ মালবী মিত্র ভস্ম হয়ে গেলেও এ জীবনে আর রমা মিত্রের হদিশ মিলবে না।
স্মৃতি যদি ফেরে
কমল গুহ আমার সহপাঠী ছিল আর প্রতিবেশী ছিল। সেই নরম বয়সে দিনের মধ্যে বেশ কয়েক ঘন্টা ওকে আটকাতে না পারলে দিনটাই জলো ঠেকত। উঁচু-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। পড়াশুনায় আমাদের পাঁচজনের থেকে অন্তত ঢের ভালো। তবু ওর জ্ঞানগম্যি সম্পর্কে আমাদের বরাবরই একটা কৌতুককর সংশয় ছিল।
মিষ্টি পাগলাটে ধরণের ছেলে। ভয়ানক খামখেয়ালী। কিন্তু গো আছে–যা ধরবে, তা করবে। মফঃস্বল কলেজ ছেড়ে কলকাতায় পড়ার সময়ও ওর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। ও ডাক্তারী পাশ করার পর একে একে গুটিপাঁচেক বড় ডাক্তারের সাকরেদি করল বছর-দুই পর্যন্ত। কিন্তু কাউকেই পছন্দ হল না। শেষে চোখ-কান বুজে বেশ কেতাদুরস্ত বড়ঘরেই একটা বিয়ে করে বসল। আমরা নেমন্তন্ন খেলাম আর ঈর্ষান্বিত চোখে ওর চকচকে বউটাকে দেখলাম। তারও মাস-তিনেক বাদে গলায় মালা-টালা দিয়ে একদিন ওকে বোম্বাইয়ের ট্রেনে তুলে দিলাম। সেখান থেকে বিলেত যাবে। ও নিজেই এক ফাঁকে বলেছিল, সেখান থেকে আরো গোটাকয়েক চটকদার ছাপ ছোপ নিয়ে আসতে পারলে একসঙ্গে তিন কাজ হবে। নিজের হিল্লে হবে, বউয়ের। মান-মর্যাদা বাড়বে আর শ্বশুরের টাকার সদগতি হবে।
তারপর দীর্ঘ দুটো যুগ কেটে গেছে। গঙ্গায় অনেক রকমের ঘোলা জল বয়ে গেছে। জীবনের ঘাটে ঘাটে ছড়িয়ে আমরা এক-একটা বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের মহড়া দিয়ে চলেছি। আমাদের ভেতর-বার দুই-ই বদলেছে। দেহের কাঠমোয় বিদায়ী মধ্যাহ্নের। ছায়া বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।
কমল রওনা হয়ে যাবার বছর-আষ্টেক বাদে এক বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম, বিদেশ থেকে ও মস্ত পাগলের ডাক্তার হয়ে, ফিরেছে। লণ্ডনে ছিল, জার্মানীতে ছিল, আমেরিকায়ও নাকি কিছুকাল ছিল।
আমি মন্তব্য করেছিলাম, ও ওর যোগ্য লাইনই বেছে নিয়েছে, কিন্তু এরপর বউটাকে ধরে রাখতে পারলে হয়!
বন্ধু প্রতিবাদ করেছিল, এতবড় মনোবিজ্ঞানী–মন বুঝে এখন তো আরো বেশি কষে বাঁধতে পারবে হে!
যুক্তির কথাই বটে। ফস করে কেন ওই উক্তি মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল নিজেই জানি না। শুনলাম, আট বছরের মধ্যে সেই প্রথম দেশে ফিরেছে সে। এই দীর্ঘকাল। অবশ্যই স্ত্রী-বিরহিত জীবনযাপন করেনি। বছর-তিনেকের মধ্যেই বউ আকাশপথে উড়ে গিয়ে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। অসুবিধে আর কী, শ্বশুরের টাকা ছিলই, তার ওপর বিদেশের কৃতী ডাক্তার হয়েছে জামাই, আর তার রোজগারের ভাগ্যও খুলে গেছে। সেই ভাগ্য দিনে দিনে নাকি আরো বিস্তারলাভ করেছে। বিদেশে অর্থাৎ লণ্ডনে আর জার্মানীতে বছর-তিনেক ঘরকন্না করেছে বউ। তারপর হাঁপ ধরে যেতে পালিয়ে এসেছে। কমল ফিরেছে তারও দুবছর বাদে।
বন্ধুর কাছ থেকে একটা বড় হোটেল-সুইটের ঠিকানা পেয়ে আমি কমলের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। দেখা হয়নি। সে তখন বম্বে না কোথায় চলে গেছে।
দেখা করতে গেছলাম বটে, কিন্তু ভেতর থেকে খুব একটা তাগিদ ছিল না। কারণ নিজের তখন লেখক-জীবনের বহু হতাশা আর অনিশ্চয়তায় ক্ষতবিক্ষত সংগ্রামী জীবন। এর মধ্যে পরিচিতজনের দুর্লভ কোনো সাফল্যের খবর কানে এলে নিজের ব্যর্থতার ছায়াটা যেন আরো বেশি ঘন হয়ে উঠতে চায়।
এর বছর-দশেক বাদে হঠাৎ আর এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা। সে মোটামুটি সফল অ্যাডভোকেট। আমারো তখন দুর্দিনের মেঘ অনেকটাই কেটেছে। অতএব পরিচিত সফল মুখ দেখলে আনন্দই হয়। দু-পাঁচ কথার পরেই সে জিজ্ঞাসা করল, আমাদের কমল গুহর খবর জানো?
বললাম, মস্ত মেন্টাল সার্জন হয়েছে, এই পর্যন্তই জানি। কেন?
–এখানেই তো ছিল কিছুদিন। আমাদের কোর্টেই ওর বউয়ের সঙ্গে মামলার নিষ্পত্তি হয়ে গেল। এ ভেরি পিসফুল ডাইভোর্স!
আমি হতভম্ব।–সে কি?
–হ্যাঁ। বউ স্যুট ফাইল করেছিল, ওর দিক থেকে কোনো বাধা আসেনি।
মস্ত পাগলের ডাক্তার হয়েছে শুনে আর এক বন্ধুর কাছে দশ বছর আগেই সেই ঠাট্টাটা বউটাকে ধরে রাখতে পারলে হয়,–এমন কাকতালীয় ভাবে ফলে যাবে। আর আমাকেই অপ্রস্তুত করবে, স্বপ্নেও ভাবিনি।
এই ঘটনা শোনার পর আরো ছবছর বাদে অর্থাৎ পাকা দুযুগ পরে কমল গুহর সঙ্গে আমার দেখা। আমাদের তখন ঠিক পঞ্চাশ চলছে।
দিন-কতকের অবকাশ পেয়ে বাংলাদেশের বাইরে এই ছিমছাম পাহাড়ী জায়গায় বেড়াতে এসেছিলাম। কমল গুহ এখানকার বিরাট পাগলের হাসপাতালের সর্বাধিনায়ক জানি–যাব যখন তার সঙ্গেও দেখা করার ইচ্ছে ছিলই।
হোটেলে উঠেছিলাম। ঠিক দুদিন বাদে বিকেলের দিকে তার রেসিডেনসিয়াল কোয়ার্টার্সের চত্বরে ঢুকে পড়লাম। বাড়ির গায়ে ওর নামের শৌখিন নেমপ্লেট, তার পিছনে একগাদা বিলিতি ডিগ্রী-ডিপ্লোমার মিছিল। দাঁড়িয়ে সেগুলো পড়ে নিলাম।
কিন্তু ওর কাছে যাবার পথ তেমন সুগম নয়। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা নেই শুনে দরোয়ান প্রথমে আমাকে দরজার কাছেই এগোতে দেবে না। আপনারজন বলতে সে স্লিপ নিয়ে যেতে রাজি হল। ছাপানো স্লিপে নামের সঙ্গে ওমুক জায়গার পুরনো বন্ধু তাও লিখে দিলাম। শুধু নামে যদি চিনতে না পেরে দেখা না করে দরোয়ানের কাছে ইজ্জত যাবে।
এতটু পরেই ডাক এলো। দরোয়ান এবারে সেলাম ঠুকে ধুতি-চাদর-পরা এই খাঁটি বাঙালীকেই বলল, যাইয়ে সাব।
ঘরে ঢুকলাম। এটা ডাক্তারের আবাসিক আপিস-ঘর। মস্ত টেবিলের একদিকের রিভলভিং চেয়ারে বসে আছে কমল গুহ। তার মুখোমুখি চার-পাঁচটা চেয়ার অন্য ভদ্রলোকদের দখলে। কোণের দিকে আলাদা ছোট টেবিলে বসে মৃদু টুকটুক শব্দে টাইপ করে চলেছে সুশ্রী একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে।
আমার দিকে এক-পলক চেয়ে থেকে একটু মাথা নাড়ল কমল গুহ। তারপর ইঙ্গিতে ভদ্রলোকদের পাশের একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল। পাইপ দাঁতে চেপে অস্ফুট স্বরে বলল, বিজ-ই ফ ফাইভ মিনিটস ওনলি, উড ইউ মাই?
আমি বোকার মত মাথা নাড়ালাম। কিন্তু সে সেটা দেখলও না বোধহয়। কেতাদুরস্ত কথা কটা বলেই ভদ্রলোকদের সঙ্গে বাক্যালাপে মগ্ন হল। হাসপাতাল-সংক্রান্ত কথা। এঁরা সকলেই এখানকার ডাক্তার বা অফিসার হবেন।
আমি ঠিক এ-রকম অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। একটু হাসি, একটু উচ্ছ্বাস না। তাদের আলোচনায় পাঁচ মিনিটের জায়গায় দশ মিনিট গেল, তার মধ্যে চব্বিশ বছর বাদে এককালের অন্তরঙ্গ কেউ এসেছে বলেও আর একবার আমার দিকে ফিরে তাকালো না। হয়ত ভুলেই গেছে। আলোচনা যাদের সঙ্গে হচ্ছে। তাদের সকলেই হয়ত বাঙালী, কিন্তু বাংলা কথা একটাও শুনলাম না। হাব-ভাব ছেড়ে কমল গুহর কথাবার্তার আধো-আধো টানগুলোর মধ্যেও পুরোদস্তুর সাহেবিয়ানা।
হয়ত সীরিয়াস আলোচনাই কিছু, কারণ বাজেট ফাইন্যান্স ইত্যাদির বাধা অনেকবার কানে এলো। তবু আমার মনে হতে লাগল, চব্বিশ বছর যখন গেছে বাদবাকি জীবনটাও দেখা না হয়ে কেটে যেতে পারত। আবার সকৌতুকে ওকে দেখছি আমি। জেনে-শুনে এখানে ওর সামনে এসে না পড়লে কে বলবে সেই কমল গুহ। আধা-গম্ভীর ভারী মুখ, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, দাঁতে মোটা পাইপ, মাথার ঝাকড়া চুলের দু-পাশে খানিকটা করে পাকা চুলের বর্ডার।
ও কে!
সর্বাধিনায়কের ছাড়পত্র পেয়ে ভদ্রলোকদের সবিনয়ে প্রস্থান। আমার নিজের অবস্থানের মেয়াদও দশ-বিশ মিনিটের বেশি হবে আশা করছি না। পাশে যে ভদ্রলোকটি তখনো দাঁড়িয়ে সে বোধহয় সেক্রেটারি। প্রভুর ইঙ্গিতে সেও প্রস্থান করল।
–মিস জোনস্!
কোণের টাইপের টেবিল থেকে সুশ্রী মেয়েটি শশব্যস্তে এদিকে ফিরল।-ইয়েস সার?
উড ইউ প্লীজ…
– অসমাপ্ত বক্তব্য বুঝে সেও টাইপ ফেলে টক-টক দ্রুত শব্দে ঘর ছেড়ে চলে গেল। কমল গুহ ততক্ষণে উঠে টেবিল ঘুরে আমার সামনে চলে এসেছে।
–ওঠ!
সম্বোধন শুনে কান জুড়লো, তবু ঈষৎ বিস্ময়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে আচমকা দু হাতে ও আমাকে বেশ জোরেই জাপটে ধরল, আর তারপরেই আমার দুগালে সশব্দে দুটো চুমু।
–তুই একটা রাসকেল, তুই একটা হতভাগা, তুই একটা ওয়াণ্ডারফুল!
একটু আগে কী চিন্তা করছিলাম ভেবে নিজেই আমি অপ্রস্তুত। হেসে বললাম, তুই পাগলের ডাক্তার হয়েছিস বটে!
হা-হা শব্দে হেসে উঠে সজোরে আমার পিঠ চাপড়ে দিল। আর তার ফলে ওর ওই পুষ্ট দুটো হাতের খুব কাছে থাকাও নিরাপদ মনে হল না আমার।
এরপর মিনিট পনের ধরে খুশির আলাপ চলল। কবে এসেছি, কোথায় উঠেছি। জেনে নিল। হোটেলের নামটা শুনে কী ভাবল একটু।–চল, ওদিকে আমার কাজও আছে একটু।
গাড়ি ও নিজেই ড্রাইভ করে দেখলাম। পাশে বসে পুরনো গল্প করতে করতে চলেছি। একটা বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে মিনিট আট দশের জন্য ও ভিতরে ঢুকে গেল। ফিরে এসে এবারে ড্রাইভ করে সোজা চলে এলো আমার হোটেলে।
এতবড় হোটেলের মালিক তাকে দেখামাত্র হন্তদন্ত হয়ে অভ্যর্থনায় এগিয়ে এলো। তার দিকে একবার সৌজন্যসূচক মাথা ঝাঁকিয়ে কমল গুহ আমার সটকে বেডিং মালপত্র যা আছে সব লোক দিয়ে তার গাড়িতে নামিয়ে দিতে বলল। আমাকে বাধা দেবার অবকাশ না দিয়ে হোটেলের মালিক তক্ষুনি ছুটল।
আমি বললাম, এটা কী-রকম হল?
জবাবে ও চোখ পাকালো, তুই একটা হতভাগা বলেছি না?
এবারে–আমি নিঃসঙ্কোচ। ওর বাইরের খোলস একেবারে বদলেছে বটে, ভিতরটা সেই চব্বিশ বছর আগের মত তাজা আর কাঁচা আছে।
সন্ধ্যের অনেক আগেই ওর বাড়িতে স্থিতি হয়ে দুজনে মুখোমুখি চায়ের টেবিলে বসেছি। রসনা পরিতৃপ্তির অঢেল আয়োজন। প্রসন্ন মুখে কমল বলল, তোর একটু অসুবিধেই হবে হয়ত
আমি মন্তব্য করলাম, অসুবিধের লক্ষণ তো দেখতে পাচ্ছি!
–সে অসুবিধের কথা বলছি না। রমণীবর্জিত, আতিথেয়তা তো তোর ভালো–ও লাগতে পারে।…ভালো কথা, বউয়ের সঙ্গে আমার ডাইভোর্স হয়ে গেছে, জানিস তো?
বিব্রত মুখে মাথা নাড়লাম।
বললাম, হঠাৎ এ-রকম একটা কাণ্ড…
-নাথিং নিউ, যেতে দে। বলছিলাম এখানে একটিও সুন্দর মুখ না দেখে তোর নীরস লাগাই স্বাভাবিক। ফেমিনাইন কার্ভস লুব্রিকেট মনোটনি।
মুখের আগল আগের থেকেও ঢিলে হয়েছে দেখছি। হেসেই জবাব দিলাম, বয়সও তো পঞ্চাশ গড়িয়ে গেল।
মুখ থেকে পাইপটা নামিয়ে ও বলে উঠল, তুই কি-রকম ছারপোকা-মার্কা সাহিত্যিক রে!…তাই বা কেন, তোর দুই-একটা বইয়েতেও তো প্রেমের বেপরোয়া কাণ্ডকারখানা দেখি!
এই ব্যস্ততার মধ্যেও পৃথিবী-চষা হোমরাচোমরা ডাক্তার আমাদের বই পড়ে বা পড়ার সময় পায় ভেবে অবাকই লাগল।
দুটো দিন বেশ কেটে গেল। ও যখন ব্যস্ত, আমি তখন হাসপাতাল দেখে বেড়াই। জীবনের রসদ খুঁজি। খোদ-কর্তার অন্তরঙ্গ বন্ধু, বাধা দেবার কেউ নেই।
তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পরে আবার লেখার কথা উঠল। কমল বলে বসল, এদেশে একালের লেখকদের মধ্যে চরিত্র খোঁজার অ্যাডভেঞ্চার নেই–দুনিয়ায় কত কাণ্ড যে ঘটে তারও খবর রাখ না তোমরা!
আমি প্রতিবাদ করলাম, যেটুকু অ্যাডভেঞ্চার করা হয়, তাইতেই তো সমালোচনা হয়–গল্পের গোরু গাছে তুলি আমরা।
ও জবাব দিল, গোরু তুললে আপত্তি কিন্তু মানুষ সত্যি সত্যি বাতাসেও ভাসে, পাতালেও ডোবে। হি অর সী হ্যাঁজ আ পেয়ার অভ ম্যাজিক উইংস-জাদু পাখা আছে দুটো করে, বুঝলে? দে ওয়ার্ক মিরাকল অ্যাণ্ড ডিভাসটেট ট্যু…বিশেষ করে মেয়েদের পাখা–দোর্জ ইন্টারন্যাল ইভস!
হেঁয়ালীর মত লাগলেও মনে মনে ধারণা, উক্তিটা এক মেয়ের প্রসঙ্গে,যে ওর ঘর ভেঙেছে। এ-কদিনে আভাসেও স্ত্রী-বিচ্ছেদের কোনো প্রসঙ্গ তোলেনি। নিরীহ মুখে বললাম, আরো একটু বিশদ না করলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।
অন্যমনস্ক একটু। তারপরেই ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়াল। মুচকি হেসে জবাব দিল, এক্ষুনি হাসপাতালে যেতে হবে, তাড়া আছে–কাল বলব–দেন ওয়ার্ক ইফ ইউ ক্যান!
আমি উদগ্রীব হয়ে সেই কালের প্রতীক্ষায় ছিলাম।
পরদিন সকাল দশটা নাগাদ হাসপাতালের একজন কর্মচারী এসে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল, সাহেব সেলাম দিয়েছে।
গেলাম। কমল বলল, চলো একটি মহিলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। সে বেশ মেজাজে আছে মনে হল, হাসছে অল্প অল্প। লিফটে উঠে আবার বলল, মহিলা যদি তোমাকে কিছু বলে, সায় দিয়ে যেও, নয়তো একটু মুশকিলে পড়তে পারো।
ওর গতকালের প্রসন্দ্রের সঙ্গে হাসপাতালের কোনো মহিলার যোগ আছে ভাবিনি। ওর স্ত্রী-বিচ্ছেদের ঘটনাই শুনব ধরে নিয়েছি। আমি লেখক, তাই কোনো বিকার বৈচিত্র্য দেখাতে নিয়ে যাচ্ছে ভাবলাম। হাসপাতালের খোদকর্তা সঙ্গে আছে যখন, আমার ঘাবড়াবার কারণ নেই।
তিনতলার ওপর পাশাপাশি গোটাকতক সুইট। একটার সঙ্গে আর একটার যোগ নেই। মাঝে মাঝে কোলাপসিবল গেটে দরোয়ান মোতায়েন। মাস গেলে যারা মোটা টাকা ফেলে দিতে পারে তাদের রোগী বা রোগিণী ভিন্ন এখানে আর কারো আশ্রয় মেলা সম্ভব নয়।
আমাকে সঙ্গে করে কমল এমনি একটা সুইটে ঢুকে গেল।
ওদিক ফিরে জানালার গরাদ ধরে আকাশ দেখছিল মহিলা। একপিঠ খোলা চুল। দুখানা বাহু, কানের দুপাশ আর পায়ের পাতা দেখেই বোঝা গেল মহিলা রূপসী। কমলের গলাখাঁকারি শুনে এদিকে ফিরল, তারপরে হেসে অভ্যর্থনা জানাতে গিয়েও আমাকে দেখে সুচারুভাবে থমকালো একটু।
আমার অনুমান মিথ্যে নয়, রূপসীই বটে। কিন্তু ফর্সা মুখের দুদিকে কালচে ছোপ, আর সুন্দর টানা চোখের কোলে কালি। সুন্দর স্বাস্থ্য,-বয়েস মন হল আটত্রিশ উনচল্লিশ হবে। পরে শুনেছি ছেচল্লিশ।
তড়বড় করে কমল আমার যে পরিচয় দিল শুনে আমারই দুচোখ কপালে ওঠার দাখিল। বলল, আমার ছেলেবেলার বন্ধু ওমুক, মস্ত ইনডাসট্রিয়ালিস্ট, বাঙালীর গর্ব বলতে পারেন। তিন চার দিন হল এখানে বেড়াতে এসেছে। এসেই পালাই-পালাই করছে কেন, বুঝলেন?
মহিলার হাসি-হাসি মুখের সুচারু অভিব্যক্তি, আমার দিকে একবার তাকিয়ে মাথা নাড়ল। কমল তেমনি তড়বড় করেই আবার বলে গেল, ওর স্ত্রী। সার্চ এ লাভলি লেডি, ওর টাকার জন্য নয়, এই জন্যেই ওকে আমার হিংসে হয়–কলকাতায় ওর বাড়ি গেলে ওই ভদ্রমহিলাকে দেখার লোভেই আর চলে আসতে ইচ্ছা করে না। ওদের দুটো ছেলে একটা মেয়ে; এখনো দুজনের টানে দুজন অন্ধ একেবারে–এই যে এখানে আছে কদিন, রোজ একটা করে মিসেসের ট্রাঙ্ক-কল, কেমন আছ, কবে আসবে।
আমারই ঘেমে ওঠার দাখিল। কিন্তু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম মহিলার দুটি আয়ত নেত্র আমার মুখের ওপর ঘন হয়ে বসতে লাগল। এই প্রথম তার চাউনিও অস্বাভাবিক ঠেকছে।
এবারে কমল মহিলার পরিচয় দিল। স্মৃতি গুপ্ত। ইনিও এখানে বেড়াতে। এসেছিলেন, জায়গাটা ভালো লেগে গেছে তাই আরও কিছুদিন থাকবেন আশা করা যায়।…এই ফাইন অ্যাকমপ্লিসড লেডি, ওঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তোমার ভাগ্য। ভালো।
আর এক দফা নমস্কার বিনিময় হল; লক্ষ্য করলাম মহিলার চোখ দুটো যেন অস্বাভাবিক চকচক করছে। কমল চট করে উঠে দাঁড়াল।–আচ্ছা আপনারা আলাপ করুন, আমি পাশের সুইট থেকে ঘুরে আসছি।
কথা শেষ করেই সে অদৃশ্য। সেই মুহূর্তেই একটা ভয় যেন আমাকে হেঁকে। ধরতে লাগল। স্মৃতি গুপ্তর চকচকে দুচোখ আরও ঘন হয়ে আমার মুখের ওপর বসছে। হঠাৎ একটু হাসল মহিলা, তার পরেই উঠে এসে অন্তরঙ্গ পরিচিতার মতই আমার গা ঘেঁষে বসল। চোখের মত সুন্দর দাঁতের সারিও ঝকঝক করে উঠল এবারে।–চারদিন হল এসেছেন, আর আজ এখানে আসার কথা মনে পড়ল?
অজ্ঞাত ত্রাসে বুকের ভেতরটা ঢিপঢিপ করছে আমার। এ কি বিড়ম্বনা রে বাবা! সন্তর্পণে ব্যবধান রচনা করতে চেষ্টা করে আর সেই সঙ্গে শুকনো ঠোঁটে হাসি ফোঁটাতে চেষ্টা করে জবাব দিলাম, সময় পেয়ে উঠিনি…।
-বলবেনই তো, আপনারা সব এই রকমই! আছেন তো কিছুদিন এখন, না স্ত্রীর টানে পালাবেন?
-না..দিনকতক থাকব।
খুশি। সামনের চুলের গোছা সরাতে গিয়ে মহিলার বাহু আমার কাঁধে ঠেকল। তারপর আর একটু ঘুরে বসার ফলে ব্যবধান সঙ্কীর্ণতর হল। উৎফুল্ল মুখে মহিলা বলে গেল, ইনডাস্ট্রিয়ালিস্টদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার আমার কত লোভ আপনি জানেন না, সত্যিকারের পুরুষকার বলতে তো তারাই। আপনাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল। একজন মানুষের মত মানুষ আমার ঘরে এলো। আমার কত ভাগ্য আজ!
নিজের ভাগ্যের কথা ভেবে আমি কঁপছি। হন্তদন্ত হয়ে তক্ষুনি কমল ঘরে ঢুকতে ঘাম দিয়ে জ্বব ছাড়ল আমার। এগিয়ে এসে ও মহিলাকে জিজ্ঞাসা করল, কেমন লাগল আমার বন্ধুকে?
–ওয়াণ্ডারফুল!
-এই জন্যেই তো নিয়ে এলাম, চলো হে আজ আর সময় নেই। বলেই সে আবার দরজার দিকে পা বাড়ালো। আমি উঠে অনুসরণ করার জন্য ব্যস্ত।
দরজার কাছে আসার আগেই পিছন থেকে খপ একটা হাত ধরে ফেলল মহিলা। কমল ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। খুব কাছে এসে ফিসফিস করে বলল, কাল আবার আসবেন, আসবেন তো? একলা আসবেন, আমি আশায় বসে থাকব –ঠিক আসবেন?
মাথা নেড়ে রাজি হয়ে ঘরের বাইরে পা দিয়ে বাঁচলাম আমি। কমল গুহ আগে আগে চলেছে। এই মূহুর্তে আমার সব থেকে রাগ হচ্ছে ওর ওপর।
ওর আপিস-ঘরে আসার পর গম্ভীর মুখে হাসি দেখলাম। জিজ্ঞাসা করল, অক্ষত আছিস?
বললাম, তোর আসতে আর দুমিনিট দেরি হলে হার্টফেল করতাম। কী ব্যাপার?
নট এ ওয়ার্ড টু-ডে, আবার কাল।
সত্রাসে বলে উঠলাম, কাল আবার ওই ঘরে?
ও হাসতে লাগল, তুই একটা কাপুরুষ-ইজন্ট সী রিয়েলি চার্মিং?
পরদিন বিকেলে কমল আবার আমাকে ধরে নিয়ে গেল। কথা দিল, আজ আর আমাকে ফেলে ঘর ছেড়ে যাবে না। তাছাড়া আমারও কৌতূহল ছিলই।
আজ দ্বিতীয় প্রস্থ বিস্ময়। গতকালের পরিচয় মহিলার মনেও নেই। কমল বলল, আমার লেখক বন্ধু, আলাপ করাতে নিয়ে এলাম। স্মৃতি গুপ্ত স্বাভাবিক মুখেই দুটি হাত জুড়ে নমস্কার করল, কি ভাগ্য, বসুন।
গলা খাটো করে কমল যেন আমি শুনছি না এইভাবে মহিলাকে বলল, লিখে আরো কত নাম করতে পারত ঠিক নেই, বাড়িতে বড় অশান্তি, বউয়ের সঙ্গে এক মুহূর্তের বনিবনা নেই…হয়ত ছাড়াছাড়িই হয়ে যাবে। বড় দুঃখের জীবন…
গতকালের বিপরীত দৃশ্য দেখলাম আমি। আমার দিকে মহিলা তাকলো একবার। আয়ত চোখে বিমনা ব্যথার ছায়া। প্রায় ফিসফিস করে কমলকে বলল, আ-হা! আমার কাছে এ-সব লোককে কেন আনেন বলুন তো, বড় মন খারাপ হয়ে যায়।
আজকের আলাপের মেয়াদ পাঁচ মিনিটও নয়। লেখার প্রসঙ্গেই দু-এক কথা জিজ্ঞাসা করল স্মৃতি গুপ্ত। আসার সময় শান্ত দুচোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, জীবনে শক্ত হয়ে যুদ্ধ করতে পারাটাও কম কথা নয়, বুঝলেন…তখন দেখবেন সব বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ হয়ে গেছে। তারপর কমলের দিকে একটু চেয়ে থেকে বলল, শুকনো দেখছি কেন, খাওয়া-দাওয়া হয়েছে, না সে-সময়ও হয় নি?
হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে কমল আমাকে নিয়ে বেরিয়ে এলো।
সন্ধ্যার পর এক পেয়ালা কফি নিয়ে বসে কমলকে বললাম, এবারে কী আমাকেই তুই পাগল করে ছাড়বি? কৌতূহল আর কত সহ্য হয়?
পাইপ ধরাবার ফাঁকে কমল হাসল একটু। আমি প্রসঙ্গ বিস্তারের আশায় আবার বললাম, মহিলাকে বেশ শিক্ষিতা মনে হলো?
–হ্যাঁ, এম-এ পাশ।…তা বয়েসকালে দেখতে কেমন ছিল মনে হয়?
জবাব দিলাম, বয়েসকাল তো এখনো মায়া কাটাতে পারে নি মনে হল।
খুশি মুখে কমল মাথা নাড়ল। তারপর খুব চাছাছোলাভাবে একেবারে সংক্ষেপে যে ঘটনাটা ব্যক্ত করল, তাই শুনে আমি স্তম্ভিত।
***
স্মৃতি গুপ্ত ইউ-পিতে থাকত। সেখান থেকেই এম-এ পাস করেছিল। তার বাবা সেখানকার ডাক্তার। ছেলেবেলায় দুই-একবার বাংলা দেশ, অর্থাৎ কলকাতা দেখেছে।
ভারী এক সুপুরুষ স্মার্ট ছেলের প্রেমে পড়ল সে। নাম পরাশর দত্ত। সেই ছেলেরও কলকাতায় ব্যবসা–ডাক্তারি সরঞ্জাম আর পঙ্গু মানুষদের সরঞ্জাম সরবরাহ করে। নিজের হেলথ ক্লিনিক আছে।
পরাশর দত্ত যখন সেখানকার কলেজের ছোকরা, স্মৃতি গুপ্তর দিকে তখন থেকেই চোখ ছিল তার। কিন্তু স্মৃতি তখন ফ্রক ছেড়ে শাড়িও ধরে নি। আলাপ ছিল, প্রেম বোঝার বয়েস তখনো সেটা নয়। কিন্তু খুব চৌকস মনে হত ছেলেটাকে তখন।
ভাগ্যের সন্ধানে পরাশর ইউ-পি ছাড়ল। আট বছর বাদে এই ইউ-পিতেই ব্যবসার কাজে এসে আবার যোগাযোগ। স্মৃতি তখন এম এ পড়ছে–সামনের বারে পরীক্ষা দেবে। আর পরাশর দত্তও তখন উঠতি অবস্থার মানুষ। দুজনে দুজনকে দেখে মুগ্ধ। স্মৃতিকে দেখে মুগ্ধ তখন অনেকেই। কিন্তু পরাশর আসাতে সকলে বরবাদ হয়ে গেল। ব্যবসার কাজে ঘন ঘন বার-দুই-তিন ইউ-পি আসার ফাঁকেই তাদের প্রেম জমাট বেঁধে গেল। তারপর বিয়ে।
স্মৃতির জীবনের সব থেকে সেরা কটা দিন কেটে গেল। পরাশর কলকাতায় ফিরল। স্মৃতি ছমাস বাদে এম-এ পাস করার পর তাকে নিয়ে যাবে। তখন পরাশর থাকে কলকাতার এক নামকরা হোটেলে। সেখানকার ঠিকানা হিসেবে একটা পোস্ট-অপিসের নাম লিখে দিল সে। তার চিঠিপত্র সব ওই পোস্ট-অফিসের কেয়ারে যায়। ব্যবসার তাগিদে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষেই ঘুরতে হয় তাকে–কখন থাকে না। থাকে ঠিক নেই। হোটেলের চিঠি মারা যায় বলে এই ব্যবস্থা।
এর পরের খানিকটা অংশ জানা গেছে পুলিশের রিপোর্ট থেকে।…অলক বিশ্বাস নামে একটা লোক সেই পোস্ট-অফিসে এসেছিল তাদের ব্যবসার অথবা সুধীর ঘোষের নামে চিঠিপত্র কী আছে সংগ্রহ করতে। পোস্ট-অফিসের লোক তাকে চেনে, সুধীর ঘোষের অনুপস্থিতিতে সেই এসে চিঠিপত্র নিয়ে যায়।
ব্যবসা এবং সুধীর ঘোষের নামে একগোছা চিঠিই ছিল। অলক বিশ্বাস দেখল তার সঙ্গে পরাশর দত্ত নামে একজনের একটা খাম ভুল করে এসে পেছৈ। খামের ওপরে মেয়েলি হাতের লেখাটা বড় সুন্দর মনে হল তার। বাইরে এসে খামটা খুলল। লিখেছে স্মৃতি নামে এক মেয়ে। বেশ চাপা উচ্ছ্বাসের ঝকঝকে চিঠি। বেশিদিন বিয়ে হয় নি বোঝা যায়।–নিজের এম-এ পাশের খবর দিয়েছে। তারপর লিখেছে, ওমুক দিন ওমুক গাড়িতে কলকাতা আসা স্থির করেছে। ছোট ভাইয়ের পরীক্ষা সামনে, তাই একলাই রওনা হতে হবে। চিঠির শেষ, পত্রপাঠ প্রাপ্তিসংবাদ পেলে আমি নিশ্চিন্ত মনে রওনা হব। তুমি অবশ্যই ঠিক সময়ে স্টেশনে থেকো। জ্ঞান-বয়সে তো কলকাতা দেখি নি, ট্রেন থেকে নেমেই তোমার মুখখানা না দেখতে পেলে তালকানা হয়ে যাব।
অলক বিশ্বাস তিন দিন বাদে স্মৃতি দত্তর ঠিকানায় একটা টেলিগ্রাম পাঠালো। পরাশর যখন দত্ত, স্মৃতিও তখন দত্তই হবে। টেলিগ্রামের বয়ান ও স্টার্ট-পরাশর।
ব্যবসার বারো আনার অংশীদার সুধীর ঘোষকে এ ব্যাপারে সে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানালো না। তাদের ব্যবসায় কৃতিত্ব ভাগাভাগি করাটা রেওয়াজ নয়। তাছাড়া সুধীর ঘোষের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে তার একটা চাপা বিরোধ চলেছে। জানলে ফোপরদালালী করবে। তারপর মেয়েটা যদি মনে ধরার মত না হয়, তাহলে ঠাট্টা-ঠিসারা করবে। কিন্তু কে জানে কেন, চিঠি পড়েই অলক বিশ্বাসের আশা, মনে ধরার মতই হবে মেয়েটা। তা যদি হয়, তাহলে সে-রকম শিকার ধরার বাড়তি প্রাপ্যও কম হবে না। অতএব পার্টনারের কাছে গোপন।
তারপরের ব্যাপারটা জল-ভাতের মত সহজে ঘটে গেল। উনিশশ সাতচল্লিশের শুরু সেটা। উদ্বাস্তুর চাপে শিয়ালদহ স্টেশন তখন নরক। কলকাতার বহু জায়গাই নরক।
ট্রেন থেকে নেমে স্মৃতি চেনা মুখ দেখল না। উদগ্রীব মুখে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। আর দূর থেকে অলক বিশ্বাসের মনে হল–এই হবে। কিন্তু রূপ দেখে সে নিজেই হকচকিয়ে গেল প্রথম; ভরসা করে তক্ষুনি সামনে এগোতে পারল না। আরো খানিক বাদে নিঃসংশয় হয়ে ব্যস্তসমস্তভাবে তার কাছে এলো।–এক্সকিউজ মি, আপনি কি মিসেস স্মৃতি দত্ত?
স্টেশনের সেই নরকের মধ্যে চেনামুখ না দেখে স্মৃতি ভয়ানক উতলা হয়ে পড়েছিল। সাগ্রহে মাথা নাড়ল।
– সরি, আমার একটু দেরি হয়ে গেল আসতে। মিস্টার দত্ত মানে পরাশর দত্ত আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি হঠাৎ বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, তাই আসতে পারলেন না…চলুন।
বেশ অসুস্থ শুনে স্মৃতি ঘাবড়ে গেল–কী অসুখ?
–পেটের নিচের দিকে খুব যন্ত্রণা, চলাফেরা করতে পারছেন না। আপনি ঘাবড়াবেন না, আসুন।
চিন্তিত মুখে স্মৃতি তার সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠল।
অলক বিশ্বাসের জীবনে আজ ভাগ্যের সূর্যোদয় যেন। বারোআনার মালিক সুধীর ঘোষ রাত সাড়ে আটটার আগে আসবে না। সাড়ে আটটার পর বাবু এসে মালিকের আসনে জাঁকিয়ে বসে টাকা গোনেন। তার ওপর আজ কোনো টোপের আশায় চন্দননগর গেছে। আগে এসে হাজির হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। ভালোই হয়েছে। এ জিনিস দেখলে কিছুদিন অন্তত আর কাউকেই সে ধারে-কাছে ঘেঁষতে দিত না। ও নিজেই একটা রাঘব বোয়াল। আর একবার বেশ সুশ্রী এক শিকার ধরে আনার পর এক মাস পর্যন্ত নিজেই তাকে গিলে বসে থাকল। এভাবে ব্যবসা চলে!…জায়গায় গিয়েই অলক বিশ্বাস অচিন্ত্য সরখেলকে টেলিফোনে আমন্ত্রণ জানাবে। অঢেল টাকার মালিক অচিন্ত্য সরখেল। সরকারী-বেসরকারী মহলে তার প্রবল প্রতাপ। কখনো বিপদের গন্ধ নাকে এলে সে-ই তাদের ত্রাণকর্তা। মেয়েটাকে একবার তার কবলে ফেলে দিতে পারলে নিশ্চিন্তি। সুধীর ঘোষ তখন নো-বডি। অচিন্ত্য সরখেলের কাছ থেকে সে আজ মোটা কিছুই খসাতে পারবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।
শৌখিন এলাকার অনেক ফ্ল্যাটের একটা বিশাল বাড়ির দোতলায় উঠে হেলথ ক্লিনিকের সাইন বোর্ড দেখল স্মৃতি। তাকে তিনতলায় নিয়ে এলো অলক বিশ্বাস। সুন্দর একটা সাজানো ঘরে এনে ঢোকালো। বাড়ির মধ্যে এটাই সাউণ্ড-প্রফ ঘর। বাইরে থেকে বা ভিতর থেকে গলা ফাটালেও দুদিকের কেউ শুনতে পাবে না।
তাকে বসতে বলে অলক বিশ্বাস বেরিয়ে গেল। পাঁচ মিনিট বাদেই এসে আবার খবর দিল, মিস্টার দত্ত গেছেন বেরিয়ামমিল এক্স-রে করাতে, তাই ফিরতে দেরি হবে। মিসেস দত্ত চা-টা খেয়ে রেস্ট নিন, চান-টান করুন, মিস্টার দত্ত ততক্ষণে এসে যাবেন।
বিভ্রাটের কথা শুনে স্মৃতির আবার মুখ শুকালো। বলল, আমাকে সেখানে নিয়ে চলুন।
অলক বিশ্বাস সবিনয়ে বলল, কোন ডাক্তারের চেম্বারে গেছেন তিনি তাদের জানা নেই।
একটু বাদে বেয়ারা চা ইত্যাদি দিয়ে গেল।–তার চাউনিটা কি-রকম বিশ্রী লাগল স্মৃতির। চা খেতে খেতে ঘরটা দেখেও অবাক লাগল একটু। সুন্দর শয্যা পাতা, বসার শৌখিন আসবাব, ড্রেসিং টেবিল, টয়লেট সেট–সবই আছে, কিন্তু ঘরে কোন বাক্স বা স্যুটকেস বা জামা-কাপড়ের চিহ্নও নেই।…ভাবল, কোথায় কোথায় ঘোরে লোকটা, তাই এ-সব রাখার জায়গারও হয়ত ঠিক নেই।
ঘরের সঙ্গে সুন্দর বাথরুম। ক্লান্তি দূর করার জন্য বেশ করে চান করে নিল। দুপুরের দিকে সত্যিই বিচলিত সে। একলাই খেয়ে নিতে হল, বেলা তিনটে বেজে। যায়–লোকটার পাত্তা নেই।
রাত হওয়া পর্যন্ত তার দুশ্চিন্তার বিবরণ বাদ দেওয়া যাক। বিকেলে বহুবার ঘর থেকে বেরুতে চেষ্টা করে দেখেছে–বাইরে থেকে বন্ধ। চিৎকার করেও সাড়া মেলে নি।
তারপর নরক। শক্তিশালী একটা জঘন্য পুরুষের সঙ্গে দিশেহারার মত ধস্তাধস্তি করতে হয়েছে তাকে। লোকটা আধঘণ্টার চেষ্টায় কাবুই করে ফেলেছিল তাকে, হঠাৎ দাঁতে করে তার বাহুর মাংস প্রায় ছিঁড়ে নেবার উপক্রম করে কয়েক মুহূর্তের জন্য মুক্তি পেয়েছিল সে। আর্তত্রাসে এবার ছুটে এসে হ্যাণ্ডেল ঘোরাতেই দরজা। খুলে গেছল। এস্ত-বসনে আলুথালু অবস্থায় পাগলের মত নিচে ছুটল।
নিচের সাজানো আপিস-ঘরে তখন সুধীর ঘোষ বসে। চার আনার পার্টনার অলক বিশ্বাস সন্ধ্যে থেকে মনের আনন্দে অঢেল মদ গিলে কোথায় নিপাত্তা হয়ে আছে জানে না। এসে অন্য লোকের মুখে শুনেছে বড় জবর শিকার ধরে এনেছে পার্টনার আজ। এবং খানিক আগে অচিন্ত সরখেল সে-ঘরে গেছে।
সিঁড়িতে অস্ফুট কাতর শব্দ শুনে কান খাড়া হল তার।
সামনে একটা আপিস-ঘর এবং আলো দেখে উদ্ধারের আসায় আত্রাসে প্রচণ্ড বেগে দরজা টেনে স্মৃতি ভিতরে ঢুকল, বাঁচান!
পরমূহুর্তে তড়িৎস্পৃষ্টের মত স্তব্ধ, পঙ্গু একেবারে। মালিকের চেয়ারে বসে আছে। পরাশর দত্ত, সহকর্মীরা সকলে যাকে জানে সুধীর ঘোষ বলে। তার সামনে মদের বোতল, মদের গেলাস–আর দুপাশে বসে দুটো মেয়ে হাসাহাসি করছে।
বিনা মেঘে বজ্রাঘাতে পরাশর দত্তও বিমূঢ়, হতচকিত। মদের নেশায় ভুল দেখছে। কিনা সেই বিভ্রম। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।–স্মৃতি তুমি! তুমি এখানে!
ভাবার অবকাশ পেলে স্মৃতি কী করত জানে না, কিন্তু সেই কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যেই বুঝি তার মাথায় সর্বনাশা কিছু ঘটে গেল। অস্ফুট আর্তনাদ করে ছুটে বেরিয়ে সোজা আবার ওপরে উঠে গেল স্মৃতি। ঠাস করে সাউণ্ড-প্রফ ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল আবার। ঘরের মধ্যে সেই আহত বাঘ বসে তখনো।
তিনতলায় উঠে পাগলের মতই পরাশর দত্ত দরজা ধাক্কাতে লাগল। দরজা খোলার জন্য চিৎকার করে ডাকাডাকি করতে লাগল। ও-ঘরে কোন শব্দ ঢুকবে না নিজেই ভুলে গেছে।
..বেশি রাতে সেই ঘর থেকে, সেই নরককুণ্ড ছেড়ে স্মৃতি অচিন্ত্য সরখেলের সঙ্গেই বেরুতে পেরেছিল। দাঁতের কামড় খেয়ে হোক বা এমন এক দুর্লভ রত্ন লাভের আনন্দে হোক, এই বারোয়ারি জায়গায় তাকে ছেড়ে যেতে অচিন্ত্য সরখেলের মন সরে নি। যাবার আগে জিজ্ঞেস করেছে, তুমি যাবে আমার সঙ্গে? ..এখানে থাকলে তোমার ওপর বেশি অত্যাচার হবে, এর থেকে তোমাকে অনেক ভালো জায়গায় রাখতে পারি।
নির্জীব কলের পুতুলের মত স্মৃতি মাথা নেড়েছে, যাবে।
পরাশর দত্ত অন্যথায় সুধীর ঘোষের চোখের ওপর দিয়েই স্মৃতিকে নিজের গাড়িতে এনে তুলেছে অচিন্ত প্রখেল। বলেছে, একটু টু-টা করলে তাকে হাজতে গিয়ে পচতে হবে।
নিস্পন্দ পরাশর দত্ত টু-টা করে নি।
হতচেতনের মত চার রাত্রি এক নামকরা হোটেলে কাটিয়েছে স্মৃতি। প্রতি সন্ধ্যায়ই অচিন্ত্য সরখেল এসেছে। যাবার আগে মোটা টাকাও গুঁজে দিয়ে গেছে। সে এত খুশি যে সর্বস্ব দিতে পারে।
তারপর মাথায় খুন চেপেছে স্মৃতির। হোটেল থেকে বেরিয়ে থানায় এসেছে। কিন্তু সুধীর ঘোষ বা পরাশর দত্ত পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে। ধরা পড়েছে অলক বিশ্বাস।
সেই থেকে দিনের পর দিন বছরের পর বছর আক্রোশের জ্বলন্ত আগুন মাথায় নিয়ে কলকাতার রাতের অভিসারে পা বাড়িয়েছে স্মৃতি দত্ত-না দত্ত নয়, তখন আগের পদবী ব্যবহার করে সে-স্মৃতি গুপ্ত। একটিমাত্র নেশা তার, সখের ঘর ভাঙাবে। অনেক ভেঙেছে–অনেক।
কিন্তু সেই সঙ্গে মাথার গোলযোগও বেড়েই চলল। শেষের দিকে এক শাসালো মাড়োয়ারীর কাছে ছিল। মস্তিষ্কের বিকৃতি অসহ্য হয়ে ওঠা সত্ত্বেও লোকটার নেশা ঘোচে নি। স্মৃতি ভালো হবে এই আশায় বহু পয়সা খরচ করে সে-ই তাকে এই হাসপাতালে রেখে যায়। কিন্তু চোখের বার হলে মনের বার, কতদিন সে আর পাগলের আশায় এই হাতির খরচ টানবে! দুবছর হয়ে গেল–সে আর খরচাপত্রও দেয় না, খবরও নেয় না।
***
কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম জানি না। এক সময় জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে এখন খরচ চালাচ্ছে কে?
নতুন করে পাইপ ধরাতে ধরাতে কমল গুহ জবাব দিল, আমি।
আমি অবাক।-তুমি কেন?
–কে জানে! একটু বিমনা দেখলাম ওকে, বলল, পিকিউলিয়ার কেস, কিন্তু সারার আশা আছে। আগের থেকে এখন অনেক ভালো।…তাছাড়া, স্ত্রীর সঙ্গে আমার ডাইভোর্সের মামলা চলছে শোনার পর থেকে এক অদ্ভুত মায়া পড়ে গেছে মহিলার–একমাত্র আমি ছাড়া হাসপাতালের আর কোন লোককে সে সহ্য করতে পারে না। ডাইভোর্স হয়ে গেছে জানার পর মায়াটা আরও বেড়েছে-আমাকে একটা অসহায় শিশু ভাবে।
আমি নীরব। বার-কয়েক পাইপে টান দিয়ে কমল হঠাৎ আমার দিকে ফিরল। –কিন্তু তারপর?
আমি তারই প্রশ্নের পুনরুক্তি করলাম, তারপর কী? উঠে ঘরের এ-মাথা ও-মাথা পায়চারি করল বার-দুই। তারপর দেশের নামজাদা। এক মনোবিজ্ঞানী ডাক্তার কমল গুহ আমার চেয়ারের সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল।আমিও তো তাই জিজ্ঞেস করছি, তারপর কী? হোয়াট নেক্সট?