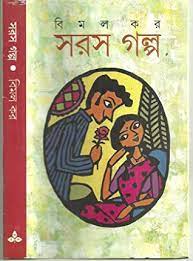অভিলাষী
জলধর মুখুজ্যে এসে বললেন, “তোমরা এখনও বসে আছ! ওদিকে যে বাসুকী ফণা নেড়েছেন।”
পশুপতি আর হাবুল সেন দাবা নিয়ে তন্ময়। সাধন একটা পুরনো রিডার্স ডাইজেস্ট নিয়ে আধশোয়া হয়ে চুরুট টানছিলেন।
মুখ তুলে সাধন বললেন, “তোমার যে কী ভাষা! যত্ত সব। হেঁয়ালি ছেড়ে কথা বলতে শিখলে না!”
জলধর তাঁর কাঁধে ঝোলানো ফ্লাস্ক নামিয়ে রেখে সোফায় বসলেন। পানের ডিবেটাও পকেট থেকে বার করে পাশে রাখলেন। বললেন, “কদম্ব মিত্তির এসেছে, সঙ্গে এবার অভিলাষী।”
কদম্ব মিত্তিরের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে পশুপতিদের দাবার ঘোড়া চাল ভুলে গেল, নৌকো টলমল করে উঠল। সাধন অবাক হয়ে বললেন, “কদম্ব মিত্তির এসেছে! কে বলল?”
“আমি বলছি, আবার কে বলবে!” জলধর বললেন।
সাধন, পশুপতি, হাবুল—মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। পশুপতি বললেন, “আসার কথা ছিল, তবে সে তো বর্ষা পড়লে।”
“বর্ষা পড়া পর্যন্ত তর সইল না,” জলধর বললেন, “আগে আগে চলে এসেছেন। অভিলাষীর ইচ্ছে।” বলে জলধর মুচকি হাসলেন। পাকা গোঁফের পাশ দিয়ে হাসিটা থুতনিতে গড়িয়ে পড়ল যেন।
পশুপতি বললেন, “অভিলাষী মানে?”
জলধর বললেন, “মেয়েছেলে!”
কয়েক মুহূর্ত সবাই কেমন হতভম্ব। তারপর নাকচোখ কুঁচকে সাধন বললেন, “ছ্যা ছ্যা! বুড়ো বয়েসে তোমার মুখ যা হয়েছে। মেয়েছেলে টেয়েছেলে কী বলছ?”
জলধর দু দণ্ড সাধনের দিকে তাকিয়ে থেকে পাঞ্জাবির পকেট থেকে একটা চিরকুট বার করলেন। বললেন, “আমার মুখকে বিশ্বাস করতে হবে না। এটা পড়ছি। শোনো।” বলে জলধর চিরকুট পড়তে লাগলেন: “জলধরবাবু, গতকাল টুয়েন্টি ওয়ান আপ-এ আমি আসিয়া পৌছিয়াছি। ঘর বাড়ি নরক হইয়া ছিল। ফকির মস্ত ফাঁকিবাজ। সে যে কিছুই করে না বুঝিতে পারিলাম। যাহা হোক, সকালে ঘরদোর ভদ্রস্থ করা গিয়াছে। আপনি অন্যদের আমার খবর জানাইবেন ও সন্ধ্যায় আসিবেন। আপনাদের এক নতুন জিনিস দেখাইব। আমার সঙ্গে এক অভিলাষী আসিয়াছেন। এমন অদ্ভুত স্ত্রীলোক আপনারা দেখেন নাই। ইহার স্পিরিচুয়াল ক্ষমতা দেখিলে অবাক হইয়া যাইবেন। পারিলে আজ সন্ধ্যায় সকলে আসুন। বাগানের ফ্রেশ টি এবং জাহাজ হইতে খালাস করা জিনিসপত্র আনিয়াছি। অপেক্ষায় থাকি। ইতি কে. ডি.।।”
দাবার চাল ভুলে পশুপতিরা জলধরের চিঠিপড়া শুনছিলেন। জলধর চিঠি পড়া শেষ করে বললেন, “নাও শুনলে তো। আর কিছু বলার আছে?”
হাবুল বললেন, “রহস্য তো আরও ঘনীভূত হয়ে গেল, জলধরদা। স্ত্রীলোক, অভিলাষী, ক্ষমতা…ব্যাপারটা কি?”
“ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার করতে হলে কদম্বকাননে যেতে হয়। চলো সবাই।”
সাধন ওয়াল-ক্লকের দিকে তাকিয়ে দেখলেন, সাতটা বাজতে চলেছে। কদম্ব মিত্তিরের বাড়ি মাইল খানেকের বেশি। হাবুল তার ছ্যাকড়া গাড়িটাও আনেনি, আনলে তবু চেষ্টা করা যেত; এখন আর এতটা পথ উজিয়ে যাওয়া যায় না। সে-বয়েস তাঁদের আর নেই, অন্তত তিনজনের, হাবুলকে বাদ দিলে অন্যরা সকলেই যাটের মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছেন, হাবুলই ষাট ধরো-ধরো করছে।
সাধন বললেন, “এখন আর কেমন করে যাবে? সাতটা বাজতে চলল। রাস্তা তো কম নয়।…তোমাকেও বলি জলধর, তুমিই বা করছিলে কী! আগেভাগে খবর দিতে পারোনি?”
জলধর বললেন “কেমন করে দেব। এই চিঠিই আমি পেয়েছি বেশ বেলায়। ফকির দিয়ে গেল। যা গরম আর লু তখন তো আর গামছা মাথায় দিয়ে বাড়ি বাড়ি খবর দেওয়া যায় না। চারটে সাড়ে চারটে পর্যন্ত লু ছুটল। তেমনি হলকা। রোদ পড়তে গা হাত ধুয়ে মুছে বেরুব, গিন্নি ঘেমেনেয়ে বমি করে এক কাণ্ড বাঁধিয়ে তুলল।”
পশুপতি ভুরু কুঁচকে বললেন, “বমি? এই বয়েসে তোমার গিন্নির বমি হয় নাকি?”
জলধর খোঁচাটা হজম করলেন না, বললেন “হয় হয়, এখনও হয়; এ গিন্নি তো প্লাস্টিকের খেলনা নয় পশুপতি, হাড়ে-মজ্জায় মেদে বিরাশি কেজি। পিঁড়ি পেতে বসলে ঘর জুড়ে যায়।…যাক যে, গরমের দিন, টক-ডাল টক দই—এ সব খেয়েছিল খুব। অম্বলে উল্টে দিল। দু ডোজ ইপিকাক দিয়ে গিন্নিকে জুত করে দিয়ে আসছি।”
পশুপতি মুখ টিপে বললেন, “বউদির কি ইপিকাক সিম্পটম?”
“তুমি কি অন্য সিম্পটম দেখেছ?”
পশুপতি হো-হো করে হেসে উঠলেন। অনন্যরাও।
হাসি থামলে হাবুল বললেন, “আজ তা হলে যাওয়া হচ্ছে না?”
“না, আজ আর কেমন করে হবে?”
“তা হলে কাল খানিকটা বিকেল বিকেল যাওয়াই ভাল।”
সায় দিলেন সবাই।
জলধর বললেন, “আমি একটা খবর পাঠিয়ে দেব মিত্তির মশাইকে; সকালেই। বিকেলে সব যাচ্ছি।”
“হ্যাঁ”, পশুপতি বললেন, “যাচ্ছি সবাই। তবে আমি ভাবছি, কদম্ব মিত্তিরের অভিলাষীকে দর্শন করতে শুধু হাতে যাই কেমন করে? বাগানে বড় সাইজের পেঁপে পেকেছে কটা, নিয়ে যাব নাকি?”
জলধর বললেন, “নিয়ে যেতে পারো। তবে অভিলাষী দর্শনের পক্ষে পাকা বেলই ভাল হত।”
হাবুল অট্টহাস্য হেসে উঠলেন। সাধনও বাদ গেলেন না। পশুপতির মুখ দেখে মনে হল, জলধরের পালটা জবাবে তাঁর প্রসন্নতা বেড়েছে ছাড়া কমেনি। ছোট করে শুধু বললেন, “তোমার গাছ থেকে ধার দিও; আমার বাগানে বাপু বেলগাছ নেই।”
আবার খানিকটা হাসাহাসি হল।
আড্ডাটা বসেছিল সাধনের বাড়িতে, বসার ঘরে। এটা হল চার প্রবীণ বা বৃদ্ধের সাবেকি আড্ডাখানা। সন্ধের মুখে রোজই বসে। অসুখ বিসুখ না থাকলে চারজনেই হাজির থাকেন। অন্য দু একজনও আসেন মাঝেসাঝে—তবে তাঁরা নিয়মিত সদস্য নন, এঁরা চারজন নিয়মিত।
সাধনবাবুর বাড়িতে মানুষ বলতে তিনি এবং তাঁর জগন্নাথ। ভদ্রলোক বিপত্নীক। জগন্নাথের হাতেই খাওয়া-পরা, ঘরদোর সংসার। সন্তান বলতে একটি মেয়ে। মেয়ে-জামাই নিজেদের বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে সংসার ফেঁদে আছে ডালমিয়ানগরে। সাধন হলেন শিষ্টগোছের মানুষ। কথা খানিকটা সমঝে বলেন; ধর্মে টান এবং মাঝারি অর্শ-ব্যামো দুই-ই দেখা দিয়েছে স্ত্রীর অবর্তমানে। চোখ দুটি আজকাল অন্যমনস্ক ও উদাস হয়ে উঠছে দিন দিন। বয়স বাষট্টি। স্বাস্থ্য মাঝারি।
সাধনের খুব ঘনিষ্ঠ হলেন জলধর। দুজনে কেমন একটা দূর সম্পর্কের আত্মীয়তাও আছে। সম্পর্কে সাধন জলধরের শালা। জলধর তড়বড়ে মানুষ। চৌষট্টি বছর বয়েসেও বাইক চাপতে পারেন, লাল আটার রুটি আর ছোলা সেদ্ধ দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারেন, তিন পোয়া দুধ এখনও রাত্রে তাঁর বরাদ্দ, গলার স্বর গমগম করে। স্বাস্থ্যটি দেখলে মনে হয় না, বয়েস তাঁকে তেমন কাবু করতে পেরেছে। গায়ের রং কালো। মাথায় বারো আনা টাক, চার আনা চুল—সবই সাদা। জলধরের সামান্য সন্ধ্যাপূজার ব্যবস্থা আছে। নিত্যই তিনি যে পেটমোটা ফ্লাস্কটি বয়ে আনেন—তার মধ্যে হরি শাহ-এর দোকানের দিশি মদ্য থাকে। একেবারে আনুপাতিক হারে জল মেশানো। এই বস্তুটি তিনি সাধনের বাড়িতে বসে খান। গল্প করেন। পান চিবোন। সিগারেট টানেন। এবং বলা বাহুল্য বৃদ্ধদের এই সান্ধ্য মজলিস সজীব করে রাখেন।
পশুপতি জলধরেরই সমবয়সী। মাস কয়েকের ছোট হতে পারেন। জলধর যখন ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেন পশুপতি তখন জিয়োলজিস্ট হিসেবে কাছাকাছি ঘোরাফেরা করেছেন। সেই সূত্রে প্রথম পরিচয়। সেই পরিচয় পরে বন্ধুত্বের পর্যায়ে দাঁড়ায়। পরস্পরের সাংসারিক কুশল বিনিময় এবং সুখ-দুঃখের পত্রালাপ চলত দূর থেকেও। অনেক পরে পশুপতি এসে বাসা বাঁধলেন এই ছোট শহরে, জলধরেরই কথায়। মানুষ হিসেবে শৌখিন, সদাশয় এবং সদাতৃপ্ত। চেহারাটি চমৎকার। বোঝা যায়—একসময়ে রূপবান পুরুষ ছিলেন। এখন আধিব্যাধি ভর করেছে, যার মধ্যে সবচেয়ে বেয়াড়া হল, হাঁপানি। বর্ষা আর প্রথম শীতটায় পশুপতি কাবু হয়ে পড়েন। হাঁপানি ছাড়া অন্য ব্যাধিটা হল ডায়েবেটিস। তবে এটা মারাত্মক নয়। পশুপতির এক ছেলে কানপুরে, অন্য ছেলে পাটনায়। বাড়িতে পশুপতি আর তাঁর স্ত্রী। জলধরের ছেলেও পাটনায়। সেদিন থেকে পশুপতি অনেকটা নিশ্চিন্ত।
হাবুল সেন—সবার চেয়ে বয়েসে ছোট। ষাটের কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছেন। বেঁটেখাটো গোলগাল চেহারা, মাথার চুলগুলো সব সাদা। খানিকটা যেন চুল পাকিয়ে বুড়োর দলে ঢুকেছেন বলে মনে হয়। ব্যবসাদার মানুষ। শেড কনস্ট্রাকশান-এর কাজে নাম আছে। ছোট ভাই ব্যবসা দেখে, আর হাবুল সেন জোগাড়যন্তর করেন। হাবুলের স্ত্রী কলকাতার কাগজে কবিতা লেখেন। হাবুল বলেন, “হিস্টিরিয়া সেরে যাবার পর থেকে ওটা হয়েছে।”সন্তানাদি নেই।
চারজনের পরিচয়টুকু মোটামুটি দিয়ে রাখা গেল। এর পর যিনি—তিনি হলেন কদম্ব মিত্তির। তাঁকে নিয়েই জলধরের সন্ধেবেলার আড্ডাখানা আজ জমে উঠল।
জলধর হাঁক ছেড়ে জগন্নাথকে গ্লাস আনতে বললেন। তারপর পশুপতিকে জিজ্ঞেস করলেন, “অভিলাষী জিনিসটা কী—তুমি জান?”
পশুপতি মাথা নাড়লেন, জানেন না।
জলধর বললেন, “সংসারে কিছুই জানলে না। তোমাদের দিয়ে কোনো উপকারটিই হল না জগতের।” বলে জলধর অবজ্ঞার মুখভঙ্গি করলেন।
পশুপতি বললেন, “তুমিই বলো। জগৎ উদ্ধার করতে তুমিই অবতার রূপে এসেছ জলধরবাবু, তুমিই বলো।”
জলধর কোনো কথা বললেন না। স্কুলে মাস্টারমশাইয়রা যেমন ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে থাকেন প্রশ্ন শুধিয়ে সেইভাবে অন্যদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন।
সাধন বললেন, “আমি কখনো কথাটা শুনিনি। স্ত্রীলোক যখন স্পিরিচুয়াল তখন উঁচু দরের কিছু হবে।”
হাবুল বললেন, “কদম্বদা এর আগে একবার এক ফিরিঙ্গি বুড়ি এনেছিলেন মনে আছে? সে নাকি কদম্বদাকে রান্না শেখাত।”
এমন সময় জগন্নাথ কাচে গ্লাস দিতে এল।
পশুপতিরা এ-সময় চা-টা খান। জগন্নাথ ইশারায় কে কে চা খাবেন জেনে নিয়ে চলে গেল।
জলধর ফ্লাস্কের ঢাকনা খুলতে খুলতে বললেন, “কদম্ব এটিকে কি-শেখাতে এনেছে কে জানে!”
পশুপতি বললেন, “শেখার কি শেষ আছে জীবনে! তা যাক, তুমি বাপু মানেটা বলো তো?”
জলধর ফ্লাস্ক থেকে হরি শা ঢেলে নিলেন। গন্ধ ছুটল। আঙুল আলতো করে গ্লাসে ডুবিয়ে আঙুল তুলে নিলেন। বার তিনেক জল ছিটিয়ে দিলেন বাতাসে। উৎসর্গ করলেন। তারপর বললেন “মানে আর কী! কদম্ব মিত্তিরের ইয়ে, মানে ওই পোষা স্ত্রীলোক গোছের কিছু। ঠিক মানেটা হাবুলের বউ জানতে পারে, পদ্য লেখে বউমা।”
পশুপতি খোঁচা মেরে বললেন, “তোমার বিদ্যেতেও কুলল না। যাক বাঁচা গেল।”
দুই
পরের দিন সন্ধের আগে আগেই চারজন কদম্ব মিত্তিরের বাড়িতে পৌঁছে গেলেন। হাবুল সেন তাঁর গাড়িটা নিয়েছিলেন। চারজনের পক্ষে যথেষ্ট। এখনও টানতে পারে বিলিতি গাড়িটা।
কদম্ব বাইরেই পায়চারি করছিলেন। মালিকে বোঝাচ্ছিলেন—বর্ষার গোড়ায় বাগানে কোন কোন গাছ লাগাতে হবে। বন্ধুদের দেখে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন, “আসুন আসুন।”
জলধর বললেন, “কালকে আর হয়ে উঠল না। আজ সব জুটিয়ে আনলাম। কেমন আছেন?”
“চমৎকার। কেমন দেখছেন আপনারা?”
“ভালই। চেহারায় ফ্রেশনেস এসেছে।”
“আসবে না! যার হাতে পড়েছি।” কদম্ব খুশি খুশি মুখ করলেন।
জলধর আর পশুপতি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। কদম্ব কার হাতে পড়েছেন বোঝা যাচ্ছে। অভিলাষীর। কিন্তু তিনি কে? কোথায় তিনি?
কদম্ব বললেন, “চলুন আমরা বসার ঘরেই বসি। বাইরে মশা।”
সাধন বললেন, “আপনার বাগানে গাছপালা বেঁচে আছে দেখছি। এবার যা গরম গেল। বিশ পঁচিশ বছরের মধ্যে এমন গরম দেখা যায়নি। মাঠঘাট খাঁখাঁ করছে মশাই, কুয়ায় জল শুকিয়ে গিয়েছে। লাস্ট উইকে দিন দুই বৃষ্টি নামল। কালবৈশাখীর পর। তাতেই যা অবস্থাটা সহ্যের মতন হয়েছে।”
কদম্ব বলল, “শুনলাম সব। আমার বাগানের বারো আনা ওই মালি সাবাড় করে দিয়েছে। এ যা দেখছেন এ হল চার আনা। দেখছেন না, আমার মতিবাগের বেলঝাড়ে ফুলের চিহ্নমাত্র নেই, দু-চারটে যা ফুটে আছে তাতে কোনো গন্ধই পাবেন না। বাগানের জন্যে আমার আলাদা কুয়ো, অবশ্য তাতে পাম্প নেই। বেটা এক বালতি জলও ঢালত না রোজ। সব কটা ফাঁকিবাজ। আসুন—।”
বাগান থেকে বারান্দা, বারান্দা দিয়ে বসার ঘরে ঢুকলেন সকলে। ততক্ষণে বাড়ির চাকর-বাকর খবর পেয়ে গেছে। ফকির এসে ঘরের আলো জ্বালিয়ে পাখা চালিয়ে দিল।
জলধর বললেন, “আপনার আসার কথা ছিল বর্ষা পড়লে, আগে আগেই চলে এলেন?”
‘বর্ষা পর্যন্ত ওয়েট করতে পারলাম না,” কদম্ব বললেন, “একটা জাহাজ ভিড়েছিল মশাই ডকে, দেড় মাস কালঘাম ছুটিয়ে দিল। এয়ার কন্ডিশনিং ইউনিট বিলকুল বরবাদ হয়ে গিয়েছে। আমাদের কোম্পানির মেকানিকদের বারো চোদ্দো ঘণ্টা করে পরিশ্রম। আমারও দুশ্চিন্তা। যা গে, কাজটা শেষ হতে মনে হল, ফিলিং টায়ার্ড। চলে এলাম।” বলে কদম্ব পকেট থেকে সিগারেট কেস বার করলেন, লাইটার, তারপর সামান্য গলা নামিয়ে স্বর পাল্টে বললেন, “তা ছাড়া উনি—মানে ওঁর ঠিক কলকাতার ভ্যাপসা গরম সহ্য হচ্ছিল না। গলায় ঘামাচি বেরুতে লাগল।”
“ওঁর মানে, এই কি যেন—অভিলাষীর?” পশুপতি বললেন।
সিগারেট কেসের ওপর একটা সিগারেট ঠুকতে ঠুকতে কদম্ব বললেন, “হ্যাঁ।”
পশুপতি আড়চোখে জলধরকে দেখলেন একবার, তারপর কদম্বকেই জিজ্ঞেস করলেন, “এখানকার গরমে আরও কষ্ট হবে না?”
“না না,” মাথা নাড়লেন কদম্ব, “এখানকার গরম ড্রাই গরম, নট লাইক বেঙ্গল। উনি তো নেপাল আর বিহার বর্ডারের মানুষ। কড়া শীত, রুক্ষ গরম—দুটোতেই মানাতে পারেন।”
হবুল বলল, “নেপালের লোক নাকি?”
“মিক্সি টাইপের!” কদম্ব সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান দিলেন, “নেপালি, বিহারি, বাঙালি, তিনেরই ট্রেস পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে সি ইজ সামথিং ভেরি স্পেশ্যাল। এমন দেখা যায় না। রেয়ার। সাম স্ট্রেঞ্জ পাওয়ার রয়েছে। সাইকিক পাওয়ার।” কদম্ব প্রশংসার গলায় বললেন।
জলধররা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।
“আপনারা একটু বসুন,” কদম্ব বললেন, “আমি আসছি।”
কদম্ব ঘর ছেড়ে চলে গেলে জলধর বললেন, “সাধন, এ যে দেখছি তে-আঁশলা। ভয়ংকর একটা কিছু হবে, কী বলো!”
সাধন কোনো জবাব দিলেন না। কদম্বর বসার ঘরের চারদিকে চোখ বোলাতে লাগলেন।
কদম্ব মিত্তির সম্পর্কে দু-চার কথা এখানে বলা দরকার। কদম্বর পোশাকি নাম কৃষ্ণধন মিত্র; ইংরেজিতে কে ডি এম; কদম্ব পুরোটা আর লেখেন না, শুধু কে ডি দিয়ে কাজ সারেন। কৃষ্ণধনের সঙ্গে কদম্বের কোনো সম্পর্ক নেই, তবু কেমন করে কদম্ব নামটা চলে গিয়েছিল বলা মুশকিল। কদম্ব দেখতে সুপুরুষ বা কুপুরুষ—কোনোটাই নয়। মাথায় সাধারণ, না লম্বা না বেঁটে; স্বাস্থ্য মাঝারি, গায়ের রং খুবই ফরসা, মাথার চুল কাঁচাপাকা এবং খানিকটা খোঁচা খোঁচা। কদম্বর চুল ছাঁটার ধরনটা হল নেভি কাট। চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমায় তাঁকে অভিজাতই দেখায়, সাজপোশাকে তাঁর বিত্তও বোঝা যায়। কদম্ব এখনও ষাটে পৌঁছননি—, তবে আর দু-চার মাস, ষাটে পৌছলেই কদম্ব কর্মজীবন থেকে ইস্তফা দিয়ে পাকাপাকিভাবে এখানে এসে বসবেন। মনে মনে এটা ছকে নিয়েই কদম্ব বছর চার পাঁচ আগে থাকতেই এই বাড়ির কাজে হাত দেন। অনেকটা জমি, ফলফুলের বাগান এবং নিরিবিলি বসবাস—এই তিন দিকেই তাঁর নজর ছিল। মোটামুটি সবই জুটেছে। টাকা থাকলে কী না জোটে। অর্থ এবং উদ্যম কদম্ব দুইই আছে।
কদম্বরা হলেন কলকাতার বনেদি পরিবার। শাখাপ্রশাখায় কদম্ব পরিবার নানা দিকে ছড়ানো, তবে কদম্ব নিজে বরাবরই খানিকটা একাকী। পিতৃদত্ত ব্যবসা ছাড়া তিনি অন্য কিছু নেননি পরিবারের, এমন কি ভবানীপুরে যে বাড়িতে থাকেন সেটাও একরকম তাঁর স্বোপার্জিত অর্থে রূপান্তর করা হয়েছে। কদম্ব হলেন ব্যাচেলার। বত্রিশ বছর বয়েসে একবার, আর চল্লিশে আর-একবার তাঁর বিয়েতে মন গিয়েছিল—কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনকে বশ করে ফেলেন। কদম্বর কলকাতার বন্ধুরা বলেন, প্রথমবার কদম্ব পাত্রীর পূর্ব প্রণয়োপাখ্যানের ইতিবৃত্ত জানতে পেরে সরে আসেন, আর দ্বিতীয়বার স্পষ্টই বুঝতে পারেন, পাত্রী তিন দাঁতের এক নকল সেট পরেন। কদম্ব এর পর আর বিয়ের দিকে ঝোঁকেননি। না ঝুঁকলেও ঘরোয়া ব্যাপারে তাঁর বেশ মন রয়েছে। যেমন ঘরদোর সাজিয়ে ফিটফাট রাখায় কদম্বর বিশেষ নজর, খাওয়া-দাওয়ায় হরেকরকম শখ, বন্ধুবান্ধবদের ডেকে ডেকে নানান ধরনের খানা তৈরি করিয়ে খাওয়াতেও ভালবাসেন, তাঁর বাড়িতে বন্ধুদের আড্ডা গল্পগুজবেরও ঢালাও ব্যবস্থা থাকে।
সোজা কথায়, কদম্ব ব্যাচেলার হলেও গৃহবিবাগী নন, তাঁর গাল তোবড়ায়নি, চোখ হলুদ হয়নি, কৌমার্যের দাঁত ভোঁতা করে তিনি দিব্যি ঘাটে এসে পা দিচ্ছেন।
মানুষটি চেহারায় তেমন চোখ জুড়োনো হয়ত নয়, কিন্তু ব্যবহারে সুজন। অহমিকা না থাক আভিজাত্য রয়েছে। সকলের সঙ্গে মেশেন না, গলাগলিও করেন না। কিন্তু পছন্দ করে যাঁদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করেছেন তাঁদের সঙ্গে আলাপে-বিলাপে কোনো আড়াল বিশেষ রাখেন না।
জলধররা হলেন কদম্বর এইরকম পছন্দের বন্ধু। এর মধ্যে জলধরই এক নম্বর ফেভারিট।
পশুপতি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।
কদম্ব ঘরে এলেন। এসে বললেন, “উনি আসছেন। সামান্য দেরি হবে। তার আগে আপনারা চা-টা খান।”
তিন
চায়ের সঙ্গে কলকাতার মিষ্টি আর ডিমের সিঙাড়া খেতে খেতে জলধর বললেন, “মিত্তিরমশাই, একটা ব্যাপারে আমাদের খটকা লেগেছে!”
কদম্ব বললেন, “কি ব্যাপার?”
জলধর পশুপতিদের দেখে নিয়ে বললেন, “এরা আমায় জিজ্ঞেস করছিল, অভিলাষী বস্তুটি কী?…আমি বললাম, স্ত্রীলোক বলে শুনেছি। তা এতে এঁদের মন ভরেনি। আপনিই বুঝিয়ে দিন এঁদের।”
কদম্ব চায়ের কাপ নামিয়ে রাখছিলেন; বললেন, “ও-একটা সেক্ট, মানে গ্রুপ। ভেরি স্মল। আপনাদের যেমন বড় বড় গ্রুপ আছে—বাউল বোস্টম সাধু সন্নেসী—ওই রকম, তবে খুব ছোট। বারসমাজি শুনেছেন, বিচারি, ছুটিয়া—এসব শুনেছেন কখনো? শোনেননি। এ-সবই আছে। তবে আগে যা ছিল তার শ্যাডো মাত্র পড়ে আছে। এরা সবাই এক একটা ছোটখাটো রিলিজিয়াস সেক্ট, বা বলুন গ্রুপ। আজকাল এদের দেখাই যায় না, রেয়ার। লোকের আর বিশ্বাস কোথায় যে বিচারি হবে, ছুটিয়া হবে। চাল ডাল সব মিলেমিশে একাকার।” বলে কদম্ব চোখের চশমাটা খুলে কোলের ওপর রাখলেন। রুমালে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, “অভিলাষীরাও ওই ক্লাসের। দেখাই যায় না আজকাল। দু চারটে পড়ে আছে।”
পশুপতি যেন বুঝতে পেরেছেন এমনভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, “কী করে এরা?”
“সাধনা। চৈতন্যের সাধনা। সুপার পাওয়ার, দি আদার ওয়ার্ড—এই সবের খোঁজ রাখে।”
“মানে, ধর্ম…”
“ধর্ম তো বটেই, তবে ওই মন্দিরে গিয়ে ঘণ্টা নাড়া নয়। এরা হল ভেতরে সাধক, পার্টলি তান্ত্রিক।”
“তান্ত্রিক?” হাবুল আঁতকে উঠল। “ওরে বাব্বা, সে তো ভয়ংকর ব্যাপার। শ্মশান, অমাবস্যা, মা কালী, শব…মড়ার মাথার খুলি…”
কদম্ব চশমাটা আবার পরে নিলেন। নিয়ে মাথা নাড়তে লাগলেন আস্তে আস্তে। হাবুলের দিকে এমন করে তাকালেন যেন ছেলেমানুষের কথায় কোনো মজা পেয়েছেন। বললেন, “না না, ওরকম ভয়ের নয়’ব্যাপারটা। তন্ত্র শুনলেই তোমাদের শ্মশান আর মাথার খুলি মনে হয়। নাথিং টু ডু উইথ দ্যাট।…আমি বোঝাবার জন্যে তন্ত্র বলিনি, আন্দাজ করার জন্যে বললুম। তন্ত্র আর তান্ত্রিক রাইটস একটা বিশাল ব্যাপার শুনেছি। আবার তান্ত্রিক গ্রুপের মধ্যেও ওরিজিন্যাল, ডুপ্লিকেট, চোরাই কতরকম কী!”
জলধর বললেন, “হ্যাঁ চোলাইও ঢুকেছে মিত্তিরসাম্বে। দু-একটা আমারও দেখা আছে বলছি। ফেগুসরাইয়ে এক তান্ত্রিক দেখেছিলাম—ছাগলের ঠ্যাং, এক কলসি চোলাই আর পিপের মতন এক ভৈরবী নিয়ে সাধনা করত। বেটা একদিন কলেরা হজম করতে গিয়ে মরে গেল।”
জলধরের কথায় সবাই হেসে উঠলেন।
কদম্ব বললেন, “ওসবের ধারে কাছে ইনি নন,” বলে আবার একটা সিগারেট ধরালেন। “ইনি অন্য ক্লাস। আমি মশাই মুখ্যু মানুষ, না পড়েছি গীতা না বাইবেল। আমার মাথায় ধম্মটম্ম ঢোকে না। তবে অভিলাষীর সঙ্গে কথা বলে যা বুঝেছি—তাতে বুঝতে পারি—ওঁদের কথা হল, এই দেহটাই হল গাছের ডালপালা; গুঁড়ি হল ইন্দ্রিয়, শেকড় হল ভেতরের প্রাণ; আর দেহ অ্যান্ড প্রাণ এই দুইয়ের মধ্যে একটা পেণ্ডুলাম ঝুলছে—তার নাম মন। মনকে একেবারে না এদিক না ওদিক করতে হবে, মানে—মানে একেবারে স্থির। সুখ দুঃখ আরাম কষ্ট কিছুই অনুভব করবে না। ওই নিস্পন্দ স্থির অবস্থা থেকে ধীরে ধীরে দেখা দেবে থার্ড কনসাসনেস, মানে আর একটা নতুন চেতনা। সেটাই হল পরম চৈতন্য, মানুষের ভেতরের পাওয়া…।”
জলধর বললেন, “ব্যাপারটা গুলিয়ে গেল মিত্তিরসাহেব। থিয়োরি অফ রিলেটিভিটির মতন। কঠিন ব্যাপার। তা কী রকম পাওয়ার বলেছেন?”
পশুপতি বললেন, “হাঁদার মতন কথা হল জলধর। পাওয়ার ইজ পাওয়ার। এ তোমার হর্স পাওয়ার নয়।”
জলধর ঠোক্কর মেরে বললেন, “নাইদার হর্স, নর ইওর চশমার পাওয়ার। ও-সব ছেলেমি বিদ্যে জানা আছে। আমাকে পাওয়ার শেখাচ্ছ!”
কদম্ব বললেন, “এই সব পাওয়ার হল একটা অন্যরকম পাওয়ার। ভেতরের পাওয়ার, সাইকিক, সাধনা করে করে পাওয়া যাচ্ছে। আসলে আমি অভিলাষীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে বুঝেছি—নরম্যাল অবস্থায় মনের যে ফাংশান থাকে সেটা রিয়েলিটির ফাংশান, কিন্তু মন যখন ওই সুপার লেভেলে চলে যায় তখন তার কাছে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান নেই—সব একাকার। মনের তখন সুপার ফাংশান। তার দেখার রে বেড়ে যায়।
সাধন বলেন, “শাস্ত্রে একেই বলেছে, মার্গ…”
জলধর দাবড়ে উঠে বললেন, “চুপ করো, শাস্ত্র কি বলেছে পরে বুঝিয়ো; এখন মিত্তিরমশাইয়ের কাছে ব্যাপারটা জানতে দাও।” জলধর কদম্ব মিত্তিরকে কখনও বলেন মিত্তিরমশাই কখনও মিত্তিরসাহেব, যখন যেটা মুখে আসে।
হাবুল বললেন, “আজকাল সুপার জেট, সুপার পাওয়ার, সুপার কনসাসনেস—সবই সুপার, তাই না পশুপতিদা?”
“ধরেছ ঠিক”, পশুপতি বললেন, “নতুন জগতটা পুরনো জগতকে আরও ছাড়িয়ে যাচ্ছে তো—তাই সুপার।”
কদম্ব সিগারেটের টুকরো ছাইদানে গুঁজতে গুঁজতে বললেন, “আমি ঘোর নাস্তিক। ঈশ্বর, যম, স্বর্গ, নরক—মায় পাপপুণ্য কোনোটাই বিশ্বাস করিনি। কিন্তু মশাই, এবার ঠকে গেলাম। অভিলাষী আমায় চমকে দিলেন। সত্যি বলছি, যেদিন ওঁকে আমি দেখলাম, গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত ইলেকট্রিক ফিলিং। গঙ্গার ঘাটে বসেছিলেন, মনে হল আমার জন্যেই এসে বসে আছেন। সঙ্গে লোক নেই, একটা পুঁটলিও নেই আশেপাশে। বললাম, থাকো কোথায়, যাবে কোথায়? অভিলাষী হেসে আঙুল দিয়ে আমায় দেখিয়ে দিলেন। বুঝলাম—আমার ঘরেই যাবেন। ব্যাস, সোজা বাড়ি নিয়ে এলাম।”
কদম্বর কথা শেষ হবার মুখে ফকির এসে বলল, “মা এসেছেন।”
চার
ফকির দরজার পরদা সরিয়ে সরে দাঁড়াল, অভিলাষী ঘরে এলেন।
জলধররা উঠে দাঁড়িয়ে অভিলাষীকে অভ্যর্থনা করবেন কিনা ভাবছিলেন—তার আগেই অভিলাষী যেন ভাব বিভোর অবস্থায় মৃদু মৃদু হাসি বিতরণ করে কোনার দিকে রাখা সোফার কাছে এগিয়ে গেলেন।
কদম্ব জলধরকে বললেন, “থাক থাক আপনাদের আর উঠতে হবে না। বসে বসেই আলাপ করুন।”
পশুপতির মনে হল, অভিলাষী প্রবীণা নয়, বৃদ্ধা নয়, পড়ন্ত যুবতী। গমনে গজেন্দ্রানী ভাব আছে এখনও।
অভিলাষী সোফায় বসলেন।
জলধররা অভিলাষীকে দেখছিলেন। অভিলাষী শাড়ি পড়েননি, আলখাল্লা ধরনের এক পোশাক পরেছেন। কোমরের তলা থেকে পোশাকটা যতটা ঢিলেঢালা কোমরের ওপর দিকটা তত নয়। কোমরের কাছে ফেট্টি বাঁধা। বুক কোমর মাপে মাপে আলগা। পোশাকের রংটা ঘন কমলা, বোধ হয় সিল্কেরই কাপড়, জেল্লা দিচ্ছিল। অভিলাষীর মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা। কপাল কান দুইই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কানে কোনো গয়না নেই। ওঁর মুখের গড়নটি অনেকটা গোল ধরনের। বড় বড় চোখ, চাপা নাক, মোটা ঠোঁট। থুতনিতে তিল রয়েছে। রং ফরসা, কেমন লালচে লালচে দেখাচ্ছিল। সিঁদুরে গাল। চোখ দুটিও সমান লালচে এবং আবেশ জড়ানো। চোখের পাতায় সুর্মার ছোঁয়া।
কদম্ব আলাপ করিয়ে দিলেন।
জলধরের সঙ্গে আলাপ করাতেই তিনি বললেন, “আপনার কথাই শুনছিলাম এতক্ষণ। দর্শন পেলাম এবার। আমাদের সৌভাগ্য।”
সাধন নমস্কার জানিয়ে বললেন, “বড় খুশি হয়েছি। আপনাদের মতন সাধক সাধিকার সাক্ষাৎ পাওয়া ভাগ্য।”
পশুপতি কদম্বকে বললেন, “আমাদের বাংলা কথা উনি বুঝবেন তো?”
কদম্ব বললেন, “বুঝবে না কেন! ওর বাংলাটাই ভাল আসে, হিন্দির চেয়ে। দু একটা ইংরিজিও জানা আছে।”
হাবুল বললেন, “মুখটা বাঙালির মতন, তাই না?”
অভিলাষী প্রায় মুদিত নয়নে হাসলেন।
কদম্ব বললেন, “বাঙালি অরিজিন। নামও তত বাঙালি।” বলে কিছু বলতে গিয়ে কদম্ব জিব কাটলেন, যেন ভুল করে নামটা বলতে যাচ্ছিলেন, আটকে নিলেন। হেসে বললেন, “অভিলাষীর গেরস্থ নাম পাঁচজনের সামনে বলতে নেই। আমার আবার ও-সব মনে থাকে না।”
অভিলাষী মাথা নাড়লেন, হাসি মুখেই। কদম্বকে নিষেধ করলেন। ইশারায়।
জলধর বললেন, “দেশ বাড়ি কোথায় ওঁর?”
কদম্ব বললেন, “আগে বলেছি না—নেপাল বিহার বর্ডার। জায়গাটার নাম বললে কেউ বুঝবে না। যোগাবানীর কাছেই। তাই না?”
অভিলাষী সামান্য মাথা হেলালেন।
পশুপতি বললেন, “কবে থেকে সাধন-ভজন শুরু হয়েছে? মানে ঘর সংসার ছেড়ে এই স্পিরিচুয়াল লাইফ?
কদম্ব বললেন, “মন্দ কি! দশ পনেরো বছর তো হবেই। তাই না?” বলে অভিলাষীর দিকে তাকালেন একবার, তারপর যেন হিসেব পাকা করে নিয়ে পশুপতিকে বললেন, “পনেরো। ফিফটিন। তার আগে একটা ইনক্যুবেশান পিরিয়ড গেছে আগে—”
“কী পিরিয়ড?”
“ইনক্যুবেশান পিরিয়ড; মানে ডিমে তা দেবার সময়। ডিম ফোটার আগে তা দিতে হয় না! স্পিরিচুয়াল ব্যাপারেও একটা তা দেবার পিরিয়ড আছে। পাঁচ সাত দশ বছর লেগে যায় কারও কারও।”
সাধন মাথা নাড়লেন। “ঠিক। ঠিক কথা।”
“এর বেলায় বছর বাইশ থেকে শুরু হয়েছিল।”
অভিলাষী সামান্য মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন।
“বাইশ থেকে সাঁইত্রিশ কি আটত্রিশ এক্কেবারে আদাজল খেয়ে অভিলাষীর ক্রিয়াকর্মে, সাধন-ভজনে কেটেছে,” কদম্ব বললেন, “তারপর আজ বছর ছয় সাত—নিজের মতন করে আছে—মানে অ্যাজ সি লাইকস।”
জলধর আর পশুপতি মনে মনে হিসেবটা কষে ফেললেন। অভিলাষীর তা হলে বয়েস দাঁড়াচ্ছে বিয়াল্লিশ। চল্লিশের ওপর ওপর পয়তাল্লিশের নীচে। গড়ন পেটন থেকে মেয়েদের বয়েস যতটা আঁচ করা সম্ভব—ততটা আঁচ করলে অভিলাষীকে এই রকমই মনে হয়। তবে আসরে নামার আগে সাজঘর ঘুরে আসায় বয়েস আরও কম কম মনে হয়।
জলধরের নজর পাকা। তিনি অভিলাষীর খুঁটিনাটি আরও কিছু দেখে নিচ্ছিলেন। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা। জলধরের মনে হল, মালার ঝুলে টান পড়েছে। তা পড়ক। দেখতে ভালই লাগে। গলায় রুদ্রাক্ষ, হাতে গালার বালা, বাঁ হাতে আংটি, চুনি বসানো। মনে হল, আঙুলের নখ চকচক করছে।
হাবুল বললেন, “আমি একবার বিন্ধাচল বেড়াতে গিয়ে এক যোগিনী দেখেছিলাম—আমার বউ যোগিনীর বড় ভক্ত হয়ে উঠেছিল। তা সত্যি বলতে কি মিত্তিরদার, সেই যোগিনীর লুক আমার ভাল লাগেনি। কেমন এক পাগলি টাইপের। মাথার জটা পেছনে হাঁটু ছড়িয়ে গেছে। তবে সেই যোগিনীর ক্ষমতা দেখেছিলাম—এক টুকরো রুটি ছুঁড়তেই দু শো ইঁদুর কোনখান থেকে বেরিয়ে এল কে জানে! আশ্চর্য!”
জলধর বললেন, “কী সাইজের ইঁদুর? ধেড়ে না লেঙটি?”
“তা মনে নেই। বড় ছোট সব ছিল।”
“তুমি কি ধাতে ছিলে, হাবুল? ভাঙা, গাঁজা খাওনি তো?”
হাবুল প্রবলভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন।
হাবুলের মাথা নাড়া দেখে পশুপতিরা হেসে উঠলেন।
এমন সময় বাইরে দমকা বাতাস উঠল। ঝড়ের মতন। কোনো ঘরের দরজা জানলা আছড়ে পড়ে বন্ধ হল, গাছপালায় শব্দ উঠল, একটা হুলো বেড়াল বাইরে কোথাও গজরাতে লাগল। সামান্য পরে সব শান্ত। দমকা বাতাস যেটুকু পড়ে থাকল তা কানে পড়ার মতন নয়।
সাধন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন তার আগেই অভিলাষী ইশারায় কদম্বকে কিছু বোঝাতে চাইলেন।
কদম্ব ঠিক বুঝতে পারলেন না। উঠে কাছে গেলেন অভিলাষীর। কিছু বললেন অভিলাষী, জড়ানো গলায়, ইঙ্গিতে। কদম্ব ফিরে এলেন নিজের জায়গায়।
“সাধনবাবু, আপনি একটু কাছে গিয়ে বসুন। কিছু বলার আছে ওর।”
সাধন বিগলিত বোধ করলেন। এত লোক থাকতে তাঁরই ডাক আগে পড়েছে। নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে অভিলাষীর কাছাকাছি একটা চেয়ারে গিয়ে বসলেন।
অভিলাষী চোখ বন্ধ করে মৃদু মৃদু দুলছিলেন। সামান্য পরে চোখ খুলে তাকিয়ে সাধনকে দেখলেন। বললেন, “দুনিয়া বড় ফাঁকা লাগে, দাদাজি?”
সাধন চমকে উঠলেন। অভিলাষীর গলার স্বর সামান্য ভাঙা ভাঙা, মোটা, জড়ানো। তা হলেও কী নরম ভঙ্গি। হাঁ করে অভিলাষীকে দেখতে লাগলেন। দু-গাল টকটক করছে। ফিকে গন্ধ চারপাশে।
সাধন বললেন, “তা লাগে! একা থাকি সংসারে। স্ত্রী আজ চার বছর নেই।”
“বিজলীবালা?”
সাধন চমকে উঠলেন। গা কেঁপে গেল। চক্ষু আর পড়ে না। হ্যাঁ। আপনি জানলেন কেমন করে?”
অভিলাষীর সেই আঙুরদানার মতন টসটসে হাসি ঠোঁটে। চোখের পাতা আরও একটু বড় করে বললেন, “রাখী পূর্ণিমায় ছেড়ে গিয়েছিলেন!”
সাধনের বুক গুমরে উঠল। অভিলাষী একেবারে ঠিক বলেছেন। রাখী পূর্ণিমাতেই বিজলী তাঁকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। চার বছর হয়ে গেল। কিন্তু অভিলাষী এত কথা বলছেন কেমন করে! আশ্চর্য!
সাধনের বুক টনটন করে উঠছিল। বিজলী বেঁচে থাকতে দামি শালের মতন যত্ন করে রেখেছিল তাঁকে। দুবারের বেশি তিনবার হাঁচলে—নাকের ওষুধ, পায়ের মোজা বার করে দিত। এখন আর কে কার!
অভিলাষী বললেন, “দুঃখ করবেন না। উনি ভাল আছেন।”
সাধন বললেন, “দুঃখ করব না। আমার তিরিশ বত্তিরিশ বছরের বউ! আপনি বলছেন কেমন করে অভিলাষী! সুখদুঃখের জীবন ভেঙে দিয়ে চলে গেল। কোথায় রেখে গেল আমাকে!”
“কেউ যায় কেউ থাকে দাদাজি!…আপনি দুখ করবেন না। উধার তো ওঁর পুনরজনম হয়ে গেল!”
“পুনরজনম। ফির জনম নিয়েছেন। এখন তো ওঁর পুরা এগারা মাস বয়েস। পুরা এগারা। তিন বছর আত্মা হয়ে ঘুমেছেন ফিরেছেন। আবার জনম নিয়েছেন।
জলধর বললেন, “এগারো মাসের বাচ্চা! আরে রামো, সে তো তা হলে কাঁথায় শুয়ে আছে পেনি পরে। দুধ তুলছে। হাতে চুষিকাঠি। সাধন, ভাবতে পারছ ব্যাপারটা! ছ্যা-হ্যা!”
সাধন চোখ বন্ধ করে দৃশ্যটা অনুমান করার চেষ্টা করছিলেন। সেই বিজলী, যার তিন গজ কাপড় লাগত সেমিজ করতে সে এখন ইয়ে হয়ে পেনিফ্রক পরে কাঁথায় শুয়ে আছে!
সাধনের দম বন্ধ হয়ে আসছিল। পুনর্জন্ম তো ডেনজারাস জিনিস। সাধন যদি সামনের দু-এক বছরের মধ্যে মারা যান—এবং চট করে জন্মান আবার, তবুও বিজলী বয়েসে বড় থেকে যাবে। তার মানে আর কোনোদিন বউ হবে না, হবে দিদি। যা কচু, এ-জন্মের বউ আসছে জন্মে…।
অভিলাষী বললেন, “আপনি কিছু ভাববেন না দাদাজি! বাচ্চি ভাল আছে, সুখে আছে।”
সাধন আর কী বলবেন? বুক ভেঙে মস্ত এক দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। এরকম তো কথা ছিল না। বিজলী বলত, কর্তা তোমার আমার বন্ধন জন্ম জন্মান্তরের, পালাবে কোথায়, যেখানেই যাও কাছা ধরে টেনে আনব।’ কই কথা তো খাটল না। এবার তুমি কী করবে বিজু! তুমি আর আমায় ধরতে পারবে না।
চোখ ছলছল করে উঠল সাধনের। একেই বলে কপাল! আমি থাকলাম এখানে পড়ে, তোমার ঘরবাড়ি আগলে, তোমার মেয়ে জামাই নাতিনাতনীর কেয়ার টেকারের মতন হয়ে, আর তুমি স্বার্থপরের মতন পালিয়ে গিয়ে আবার একদফা জন্ম নিয়ে কাঁথায় শুয়ে পা ছুঁড়ছ। নিকুচি করেছে জন্মান্তরের!
সাধন চোখের জল মুছতে রুমাল হাতড়াচ্ছিলেন।
এমন সময় অভিলাষীর গলা শোনা গেল। এবার একটু জোরালো হয়েছে।
“পায়ে ছ’টা আঙলি কার আছে?” অভিলাষী বললেন।
জলধর থ’ মেরে গেলেন। নিজের পায়ের দিকে তাকালেন। ধুতিতে ঢাকা। বললেন, “আমার।”
“ডান পায়ে?”
“হ্যাঁ।”
“পিঠে ঘা আছে? কারুয়া ঘা।”
“কার্বাঙ্কোল হয়েছিল। গত বছর।”
“রাতমে ঘুম হয়?”
“তোফা। এক আধদিন পেটে গ্যাস হলে ঘুম গড়বড় করে।”
“চিন্তাউন্তা নেই?”
“কিসের চিন্তা! আমার হল আপনি আর কোপনি। তা অভিলাষীজি, সাধনের পরিবারের কথা হল—এবার আমার ইয়ের কোন দশা হবে বলুন তো?” জলধর যেন ঠাট্টার মতন করে বললেন, যদিও তাঁর কোথায় সামান্য খটকা লাগছিল। জলধরের ডান পায়ে কড়ে আঙুল দুটো, আর পিঠে এক কার্বাঙ্কল হয়ে গত বছর গরমের সময় বেজায় ভুগেছিল। অভিলাষী এসব কথা জানল কেমন করে?
অভিলাষী চোখ বুজে বসে থাকতে থাকতে একবার নাকের বাঁ দিক টিপলেন, তারপর ডান দিক। দেওয়ালের ছবির আড়াল থেকে টিকটিকি ডেকে উঠল।
অভিলাষী বললেন, “চুহা, কাউয়া, বিললি—তিন জানোয়ার তু পাললি। চুহা তো আপনি জানেন জলধরজি, ইঁদুর। কাউয়া—কাক। ইঁদুর কাক আর বিললি তিন জানোয়ার সব ঘরমে থাকে আগর না থাকে তো আগ লাগে। আপনার ঘরে চুহা নেই?”
জলধর খানিকটা থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন, বললেন, “ধেড়ে ধেড়ে ইঁদুর আছে। গিন্নির পায়ে একবার কামড়ে দিয়েছিল। ইনজেকশান দিতে হয়েছিল, অভিলাষীজি।”
“কাউয়া নেই?”
“কাউয়া কি কেউ পোষে। কাক আর ইঁদুর সব বাড়িতেই আছে।”
অভিলাষী একটু যেন হাসলেন, “ঠিক বলেছেন। এবার একটা কথা বুঝে নিন। মানুষমে তিন ইন্দ্রিয় জাদা জাদা কাম করে। চুহা হল কাম, কাউয়া হল ক্রোধ, আর বিললি হল লালচ।”
পশুপতি মুগ্ধ হয়ে বলল, “ব্রিলিয়ান্ট। অভিলাষী দারুণ বলেছেন। জলধরের তিন ইন্দ্রিয়ই তেজি…।”
জলধর ধমকে উঠতে যাচ্ছিলেন তার আগেই অভিলাষী বললেন, “জোর হলে আরও তিন জনম।”
“তিন জন্ম?”।
“আগাড়ি জনম আর চুহাগিরি করবেন না!”
জলধর চট করে একবার পশুপতির দিকে তাকিয়ে নিলেন। “এ-জন্মেই করলাম তো আগাড়ি জনম!”
অভিলাষী বললেন, “ঝুট বলছেন।”
“ঝুট! কোন শালা আমার নামে বলে—!”
নিরীহ মুখ করে পশুপতি বললেন, “কোনো শালাই বলবে না। জলধরের ও-সব ফালতু দোষ নেই অভিলাষীজি। লোকে যে বলে, জলধর মধু কবিরাজের বিধবা শালীর সঙ্গে…”
“অ্যাই, হচ্ছে কি?”
“কথাটা শেষ করতে দাও না,” পশুপতি বললেন, তারপর অভিলাষীর দিকে তাকালেন। “শুনুন অভিলাষীজি! মধু কবিরাজের বিধবা শালী এখানে বেড়াতে এসে ছ’ আট মাস ছিল। গানের লাইনের লোক তো, গজল গাইত। বেনারসি না এলাহাবাদি বিবি। আমাদের জলধর কবিরাজের বাড়ি গিয়ে গানের সঙ্গে ঠেকা দিত তবলায়। জলধর ভাল তবলচি!…আমি মিথ্যে বলছি না অভিলাষীজি, মিত্তির সাহেব সাক্ষী।”
অভিলাষী মুচকি হেসে বললেন, “জলধরজি বড়া কলাচার।”
জলধর ক্ষেপে গিয়ে বললেন, “তবলার কথা থাক। আপনি বলুন তো, কে থাকছে কে যাচ্ছে! আমি আগে, না গিন্নি আগে?”
“ভগবান জানেন।”
“ভগবান জানেন তো আপনি কী জানেন?”
“আমি আঁখ বন্ধ করে এক তামাশা দেখছি, জলধরজি! দূরমে রামলীলা হচ্ছে। সীতাজি কাঁদছেন, হনুমানজি হায় হায় করছেন।”
জলধরের বুক কেঁপে উঠল। বলে কি অভিলাষী! তবে কি তাঁর দশাও সাধনের মতন হবে?
জলধর বললেন, “শুনুন অভিলাষীজি! আমি সাফসুফ বলে দিচ্ছি—আই অ্যাম নট সাধন! চিরটাকাল আমি সামনে সামনে এসেছি—গিন্নি আমার পেছন পেছন। ফাইন্যাল রাউন্ডেও অমি আগে যাব। বুঝলেন।”
সাধন বললেন, “যাওয়া কি তোমার হাতে?”
জলধর বললেন, “দেখা যাবে। এখন পাঁচ সাত বছর যাচ্ছি না। পরের কথা পরে।…তা মিত্তিরমশাই আমাদের তো রাত হয়ে যাচ্ছে, এখন শুরু করলে—!” বলে ইশারায় পানভোজনের কথা বুঝিয়ে দিলেন।
খেয়াল হল কদম্বর। বললেন, “তাই তো সাতটা বেজে গেল। ফকিরকে ডাকি।’
হাবুল বললেন, “আমরা যে বাদ পড়ে গেলাম, কদম্বদা।”
“হবে হবে, অভিলাষী তো পালিয়ে যাচ্ছে না। আবার একদিন হবে। ওর শরীর ভাল যাচ্ছে না। একদিনে বেশি স্ট্রেন উচিত নয়।”
হাবুল অভিলাষীর দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়লেন। “ঠিক আছে, তাই হবে। আমাদের একটু মনে রাখবেন অভিলাষী দিদি।”
অভিলাষী মাথা হেলিয়ে হাসলেন। তারপর উঠে দাঁড়ালেন। চলে যাচ্ছিলেন অভিলাষী, সামান্য দুলছেন। পায়ে খড়ম-জুতো। ঠুক টুক আওয়াজ উঠছিল। পশুপতির পাশ দিয়ে যাবার সময় অভিলাষী আড়চোখে কেমন করে যেন ইশারা করলেন। অন্য কেউ নজর করল না। পশুপতি হাত জোড় করে বলল, “আপনি ভগবতী। কাল পরশুই আবার আসব।”
পাঁচ
ফিরতে ফিরতে রাত ন’টা।
হাবুল আর সাধন সামনে। পেছনের সিটে পশুপতি আর জলধর। জলধর যেভাবে গাড়ির মধ্যে গড়িয়ে রয়েছেন তাতে বোঝা যায় তিনি বাস্তবিকই এখন জলে পূর্ণ হয়ে রয়েছেন। তাঁর চোখ বোজা। মাঝে মাঝে নাক ডাকছিল।
পশুপতি হুঁশে আছেন—তবে এলিয়ে আছেন।
সাধন সামান্য মুখে দিয়েছেন তাতেই নেশা ধরে গিয়েছে। মাঝে মাঝেই তাঁর শোক উথলে উঠছে।
হাবুল যতটুকু নেশা করেছিল তাতেই আনাড়ির মতন গাড়ি চালাচ্ছিল। ভাগ্যিস মেঠো জমি আশেপাশে, নয়ত গাড়ি ডোবায় গিয়ে পড়ত।
সবাই চুপচাপ। হাবুল নিজেকে সজাগ রাখার জন্যে জোরে জোরে জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলছিল।
হঠাৎ হাবুল বলল, “জলধরদা কি ঘুমিয়ে পড়েছেন?”
কোনো সাড়া নেই।
পশুপতি আড়ষ্ট জিবে বললেন, “একেবারে কাদা। কাছা খুলে খেয়েছে। ওকেই আগে নামিয়ে দিও হাবুল। চ্যাংদোলা করে নামাতে হবে।”
হঠাৎ জলধর বসা গলায় বললেন, “আমি ঘুমোইনি।”
“ঘুমোওনি! নাক ডাকছ যে!”
“জেগে জেগেও নাক ডাকা যায়। আমি ভাবছিলাম।” জলধরের কথাগুলো অস্পষ্ট, জড়ানো।
“কী ভাবছিলে?”
“অভিলাষীকে ভাবছিলাম। মুখটা আমার বড় চেনা চেনা লাগছে। কোথায় যেন দেখেছি।”
পশুপতি বললেন, “দেখেছ?”
জলধর কোনো জবাব দিলেন না।
আরও খানিকটা এগিয়ে আসার পর সাধন আবার যখন ফুপিয়ে কেঁদে উঠছেন হঠাৎ যেন জলধর কিছু আবিষ্কার করলেন। বললেন, “পশুপতি, এই অভিলাষী আর মধু কবিরাজের সেই বিধবা শালীটা এক নয়? সে বেটি হাওয়া হয়ে গেল—হঠাৎ। কদম্ব তখন এখানে এসেছিল। কদম্ব যাবার হপ্তা খানেক পরে ও-বেটি পালাল। তাই না?”
পশুপতি বললেন, “তুমি কোন বিধবার কথা বলছ? যার গানের সঙ্গে তবলায় ঠেকা দিতে যেতে। বাঁজা বিধবা।”
সিটের গর্ত থেকে উঠতে উঠতে জলধর বললেন, “মেয়েছেলে কেমন ভোল পালটেছে দেখেছ! ছিল কলসী, হয়ে গেল অভিলাষী। চেনাই যায় না। তাই বলি অভিলাষী এত হাঁড়ির কথা বার করছে কেমন করে? কদম্ব মিত্তির এমন পাকা ধড়িবাজ তা জানতাম না। যাক ভালই করেছে। বুড়ো বয়েসে একটা অবলম্বন তো দরকার। কি বলো?”
পশুপতি কিছু বলার আগেই হাবুলের গাড়ি গড়িয়ে গড়িয়ে মাঠে নেমে গেল।
আত্মাদর্শন
“এই দেখো হে কাকে এনেছি সঙ্গে করে,” বলে রমেশবাবু সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠে পেছনের মানুষটিকে দেখালেন।
জগবন্ধু বেতের চেয়ারে বসে পা তুলে মোজা পরছিলেন। চেয়ারের পাশে কেডস জুতো। পায়ের আধখানায় মোজা উঠেছে। বললেন, “দেখছি তো, কাকে ধরে নিয়ে আসছ! উনি কে?”
জগবন্ধু চিনতে পারলেন না। বাগানের ফটক খুলে রমেশের সঙ্গে কথা বলতে বলতে যে ভদ্রলোক আসছিলেন তাঁর দিকে জগবন্ধুর চোখ আগেই পড়েছিল। বাবাজি-বাবাজি গোছের চেহারা। দাড়ি, গোঁফ, ঘাড় পর্যন্ত বাবরি চুল। আনা আষ্টেক সাদা হয়ে এসেছে। ভদ্রলোকের শরীরের গড়ন-পেটন দোহারা, রঙ বোঝা যাচ্ছিল না, কালো অবশ্য নয়।
মাথা নাড়লেন জগবন্ধু। বাবাজিকে চিনতে পারছেন না।
রমেশ বললেন, “পারলে না? আমাদের বঙ্কু। নন্দবাবুর ছেলে গো। সেই ডাক্তার নন্দবাবু, বরফ কলের কাছে দোতালা বাড়ি।”
“বঙ্কু!” জগবন্ধু, একে একে বরফ কল, নন্দ ডাক্তার, এবং খাকি হাফ প্যান্ট পরা বঙ্কুকে ঠাওর করে নিতে পারলেন, কিন্তু এই দাড়ি গোঁফঅলা, বাবরি চুলের বঙ্কুকে তার সঙ্গে মেলাতে পারলেন না। ঢোক গিলে বললেন, “তা ওর এই দশা কেন?”
রমেশ বললেন, “বঙ্কু এখন স্পিরিচুয়ালিস্ট। আত্মা ভূত প্রেত, পরকাল-টরকাল নিয়ে পড়ে আছে।”
“কেন, ওর কি বউ মারা গেছে?” জগবন্ধু বললেন, বলে গোড়ালির কাছ থেকে মোজাটা পায়ের ওপর দিকে টেনে নিলেন।
বঙ্কু মোলায়েম করে হাসল। বলল, “ভাল আছেন, জগুদা?”
“যে বয়সে যেমন থাকে ভাই সেই রকম আছি। অল্পস্বল্প ডায়েবেটিস, প্রেশারের খানিকটা ট্রাবল, হাতের গাঁটে আরথারাইটিস—এই সব উপসর্গ নিয়ে আছি। তা তুমি দাঁড়িয়ে কেন? বসো?”
“আজ আর বসব না। আপনারা তো এখন বেড়াতে বেরুবেন।”
“ওই একটা চক্কর। মোল্লার দৌড় মসজিদ। স্টেশনের দিকে যাব একবার। কলকাতার গাড়ি এলে খবরের কাগজটা নেব, একটা পাউরুটি, এক প্যাকেট সিগারেট, গিন্নির জন্য সেউভাজা। তারপর আবার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরব।”
“কেমন লাগছে জায়গাটা?”
জগবন্ধু আঙুল দিয়ে রমেশকে দেখালেন। “ওকে জিজ্ঞেস করো। ও হল ইঞ্জিন, আমি মালগাড়ি। নিজের বউ, আমার বউ—দুটো বউকে মন্তর দিয়ে জপিয়ে হাওয়া বদলাতে নিয়ে এসেছে আমাকে। আমার তো দেখছি একদিন খিদে হলে দু দিন পেট একেবারে ফায়ার ব্রিকস হয়ে থাকে। কুয়োর জলে চান করে করে গায়ে রাশ বেরিয়ে গেল। এটা কি কোনো ভদ্রলোকের জায়গা।”
রমেশ বললেন, “বঙ্কু, তুমি একবার সকালের দিকে এসে জগোবাবুকে দেখো। চোখের তলা লাল হয়ে গিয়েছে, গাল টকটক করছে…। নবযৌবন সঞ্চার হচ্ছে সিক্সটি টুতে।”
“সে কি তোমার জলের গুণে? চার আউন্স করে ওষুধ খাই না সন্ধ্যেবেলায়? বিলিতি ওষুধ। কাস্টমস থেকে যোগাড় করে আনতে হয়েছে?”
বঙ্কু এবার জোরেই হাসল।
রমেশ বললেন, “চলো, তা হলে বেড়ানোটা সেরে আসি। বঙ্কু, তুমি একটু বসো, আমি একবার ভেতর থেকে ঘুরে আসি। গিন্নিদের ফরমাসটা শুনে নেওয়াই ভাল। ও, একটা কথা তোমায় বলতে ভুলে গিয়েছি। জগোবাবুর গিন্নি সম্পর্কে আমার বড় শালী, মাসতুতো শালী।” বলে অন্দরমহলে চলে গেলেন।
জগবন্ধু অন্য পায়ের মোজাটা পরতে পরতে বললেন, “কোন ছেলেবেলায় তোমায় দেখেছি, বঙ্কু ; তারপর এতকাল পরে ; আফটার ফরটি, ফটি ফাইভ ইয়ার্স কি বলো? চেনা মুশকিল। রমেশ তোমায় চিনল কেমন করে?”
“এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল, অন্য দু একজন ছিলেন। কথায় কথায় ধানবাদের কথা উঠল, তাতেই চিনলেন।”
“বাহাদুরি আছে রমেশের।” মোজাটা পরে ফেললেন জগবন্ধু। “তা তোমার বাবা মা?”
“নেই।”
“সেই যে দিদি ছিল, কি নাম যেন…বয়েসে সব ভুলে যাই হে।”
“দিদিও নেই।”
জগবন্ধু সহানুভূতির শব্দ করলেন। “সবই হারিয়েছে?’
“তা বলতে পারেন,” বঙ্কু নিস্পৃহ গলায় বলল।
কেডস পায়ে গলিয়ে নিলেন জগবন্ধু। “সংসার টংসার করোনি? বউ ছেলেমেয়ে?”
বঙ্কু দাড়িতে হাত রেখে বলল, “করার চেষ্টা করেছিলাম। ছেলেমেয়ে হয়নি। বউ খসে গেছে।”
এমন সময় জগবন্ধুর স্ত্রী যামিনীকুসুম এলেন। বিকেলের গা-ধোওয়া কাপড় বদলানো গিন্নি গিন্নি চেহারা। এসেই একবার বঙ্কুকে দেখে নিয়ে মুখভরা হাসি খেলিয়ে বললেন, “ঠাকুরপোর মুখে সব শুনলুম, ভাই। আপনিও সম্পর্কে আমাদের দেওর। এ বাড়িতে যখন পা দিয়েছেন একটু চা খেয়ে যান।”
বঙ্কু নমস্কার করে বলল, “আমরা একই জায়গার লোক, বউদি। ছেলেবেলাটা একসঙ্গে কেটেছে। অনেককাল পরে দেখা হল। বড় ভাল লাগল। চা আজ থাক না, পরে একদিন হবে। জগুদারা এখন বেড়াতে যাবেন, কার্তিক মাস, বিকেল তো ফুরিয়ে গেল।”
“তা যান না ; আপনি দু দণ্ড বসেই যাবেন। আশা চা নিয়ে আসছে।”
জগবন্ধু জুতোর ফিতে বেঁধে ফেললেন। “চা-টা খেয়েই নাও, তারপর এক সঙ্গে বেরিয়ে গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে।”
বঙ্কু মাথা হেলাল।
যামিনী বললেন, “শুনলুম আপনি এখানে আশ্রম করেছেন?”
“আশ্রম ঠিক নয়” বঙ্কু বলল, “বলতে পারেন আশ্রমের মতন। মন্দির ঠাকুর দেবতা নেই। পুজো পাঠও হয় না।”
জগবন্ধু গিন্নির দিকে তাকিয়ে বললেন, “বঙ্কু স্পিরিচুয়ালিস্ট। আত্মা নিয়ে কাজকর্ম করে। বড় কঠিন সাধনা। থিয়োসফি বোঝ?”
যামিনী পিঠের আঁচল সামলে বললেন, “বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা আছে সব তুমিই বোঝ? কত আমার ওজনদার!” বলে অবহেলায় স্বামীকে বাক্যবাণ হেনে বঙ্কুর দিকে তাকিয়ে বললেন, “ঠাকুরপো বলছিল আপনার নাকি অপদেবতা ধরার ক্ষমতা আছে। সত্যি নাকি?”
ছেলে ভোলানো হাসি হেসে বঙ্কু বলল, “অপদেবতা নয়, আত্মা।”
“ওই হল। ভূত তো?”
“ভূত হল নিচু স্তরের আত্মা। স্কুলে যেমন ওয়ান টু ক্লাস—ভূত হল সেই ক্লাসের। আত্মারা হলেন অনেক উঁচু ক্লাসের।”
জগবন্ধু ঠাট্টা করে বললেন, “হ্যাঁ গ্র্যাজুয়েট, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের।”
যামিনী কৌতূহল চেপে রাখতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, “আত্মারা ক্ষতি করেন না? আপদ বিপদ হয় না?”
“না, না, মোটেই নয়।”
“দেখতে বড় ইচ্ছে করে। ভয়ও হয়।”
“বেশ তো, দেখবেন। দেখাব। ভয়ের কিছু নেই।”
চা নিয়ে আশালতা হাজির হলেন। পেছনে রমেশ।
স্পিরিচুয়ালিস্ট বঙ্কুকে যামিনীর খুব পছন্দ হয়ে গেল। কথায় বার্তায় নম্র, নিজে বেশি কথা বলে না, মুখে হাসিটি লেগে আছে, যখনই এ-বাড়িতে আসে কিছু না কিছু হাতে নিয়ে ঢোকে। যামিনী রাগ করেন, এ তুমি বড় অন্যায় করছ বড় ঠাকুরপো, এমন করলে তোমায় আর বাড়ি ঢুকতে দেব না। বঙ্কু এখন যামিনীর কাছে তুমি হয়ে গিয়েছে। যামিনী রাগ করলে বঙ্কু বলে, নিজের বলতে আমার কেউ কোথাও নেই বউদি ; আপনারা আমার আত্মীয়ের মতন। কদিনের জন্যে বেড়াতে এসেছেন, সামান্য কিছু হাতে করে আনলে আনন্দ পাই। এতে কেন বাধ সাধবেন।’ এরপর যামিনীর মুখ বন্ধ হয়ে যায়।
আশালতা বরাবরই খানিকটা ভিতু গোছের মানুষ। বঙ্কু ভূতভজনা করে শুনে তাঁর রীতিমত ভয় ধরে গিয়েছিল গোড়ায়। বঙ্কুর ব্যবহার দেখে, কথাবার্তা শুনে সে ভয় কেটে গেল বারো আনা। এখন তিনি বঙ্কুর চায়ে চিনি বেশি দেন, সকালে মিষ্টিমাষ্টা এলে কালাকাঁদ, কালোজাম দু চারটে সন্ধের জন্যে রেখে দেন; বঙ্কু এলে সাজিয়ে দেন। ভেজিটেবল চপ করে খাওয়ান। বঙ্কু নিরামিষাশী।
রমেশ বঙ্কুর সঙ্গে বেশ জমিয়ে ফেলেছেন। নিজেদের ছেলেবেলার গল্পগুজব ছাড়াও হরেক রকম আলোচনা হয় ; এখানকার ক্লাইমেট, জমির দাম, বাড়ি করার খরচ থেকে শুরু করে দেশের হালচাল ; ব্ল্যাক মানি, ভেজাল, ইন্দিরা, সাঁইবাবা—মায় মঙ্গল গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব আছে কিনা তারও আলোচনা চলে।
এক জগবন্ধুই বঙ্কুকে একটু তফাতে রাখতেন। তিনি যে মানুষ খারাপ তা অবশ্য নয়, কিন্তু এ-বাড়িতে বঙ্কুর এতটা সমাদর তাঁর পছন্দ হত না। চেনাজানা মানুষ বঙ্কু, ছেলেবেলার পরিচয়, ছোট ভাইয়ের মতনই অনেকটা, তাকে বাড়িতে ডেকে চা মিষ্টি খাওয়াও, গল্পগুজব কর—আপত্তি নেই, তা বলে মাথায় তোলার দরকারটা কী? জগবন্ধু নিজেও কি হাসি তামাশা, গল্পগুজব করেন না বঙ্কুর সঙ্গে, কিন্তু যামিনী বঙ্কুকে দেখলেই যেন আহ্লাদে গলে যায়, কত কথা—সংসারের কোনো কথাই বাদ যায় না। রমেশটাও তাই। এই দুজনে মিলে হাঁড়ির সব খবরই বার করে দিয়েছে বঙ্কুর কাছে। নিজেদের ছেলেমেয়েরা কে কি করছে, কার কোথায় বনিবনা হচ্ছে না, মেয়ে নিজের পছন্দে বিয়ে করল, ছেলের বউ সকালে ঘুম থেকে উঠে লিপস্টিক মাখে—এ-সব কথা বলার কি কোনো দরকার ছিল?
সেদিন বসার ঘরে বসে গল্প হতে হতে রাত হল। জগবন্ধুর ওষুধ খাবার সময় হয়েছে। আটটায় শুরু করলে ন-টায় শেষ হবে। একটু জিরেন দিয়ে রাত্রের খাওয়াদাওয়া। জগবন্ধু উসখুস করছিলেন। শেষে বঙ্কুকে বললেন, “ওহে প্রেতসিদ্ধ, আমি এবার উঠি। রাতও হচ্ছে।”
যামিনী বললেন, “উঠবে কেন? বসো। কথাটা ঠিক হয়ে যাক।”
“কিসের কথা?”
“এতক্ষণ কি ঘুমোচ্ছিলে? সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা রামের মা। জ্বালালে বাপু। বঙ্কু ঠাকুরপোর ওখানে আমরা কবে যাচ্ছি। কাল না পরশু?”
“গেলেই হয়, এ নিয়ে ভাববার কি আছে?”
“যথেষ্ট আছে। ফুরফুরে হাওয়া খেতে তো যাচ্ছি না, যাব ওই আত্মাদের দেখতে। কাল শনিবার। তার ওপর কৃষ্ণপক্ষ। কাল আমার সাহস হয় না।”
“আত্মাদের কোনো বার নেই, কি বলো বঙ্কু?” রমেশ বললেন।
“আত্মা আমাদের অধীন নয়, রমাদা, তাঁরা নিজেদের ইচ্ছায় আসেন যান। অভিরুচি হলে দেখা দেন, না হলে দেন না। শনি সোম বলে কথা নেই।”
“তা হোক। শনিবারে আমি যাব না,” আশালতা বললেন।
“তবে পরশু রবিবার।” যামিনী দিন ঠিক করে ফেললেন। বঙ্কুর আশ্রমে চার জনে আত্মা দেখতে যাবেন। দেখা তো যাবে না, গলা শোনা যাবে, আর যদি গলাও না শোনা যায় পেন্সিলের লেখা ফুটবে। বঙ্কু তাই বলেছে।
আসর ভাঙল। বঙ্কু চলে গেল। জগবন্ধু খেপে গিয়ে বললেন, “ভূতো বঙ্কুর ধাপ্পায় তোমরা ভুললে। বেটা আত্মার আ জানে। তোমরা যাচ্ছ যাও, আমি যাব না।”
যামিনী সরবে বললেন, “যাবে না মানে। নিশ্চয় যাবে।”
রবিবার চার জনে শেষ বিকেলে বঙ্কুর বাড়ি হজির হলেন। আধ মাইলটাক একটানা হেঁটে এসে যামিনীর গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। বাড়িতে পা দিয়েই যামিনী জল খেতে চাইলেন ; বললেন, “এই তোমার আশ্রম। বড় নিরিবিলি তো?”
বঙ্কু বাইরের বারান্দায় চেয়ার বেঞ্চি সাজিয়ে আসন পেতে রেখেছিল। চার জনকে খাতির করে বসাল। নিজের হাতে জল এনে দিল যামিনীকে। জগবন্ধু বললেন, “তোমার আত্মাদের কখন আসতে বলেছ হে? আটটা নাগাদ আমাদের ফিরতে হবে।”
বঙ্কু বলল, “একটু বসুন। জিরিয়ে নিন। চা খান।”
“ওই করতেই তো সন্ধে হয়ে যাবে। অন্ধকার হয়ে আসছে—দেখছ না!”
রমেশ বললেন, “না না, তাড়ার কিছু নেই বঙ্কু! রাত হয় হবে। যা দেখতে এসেছি সেটা বাপু না দেখে যাব না। কি বলো দিদি?”
যামিনী সায় দিয়ে বললেন, “ঠিকই তো!” বলে স্বামীর দিকে তাকিয়ে ধমক দিলেন, “সবাই তোমার হুকুমের চাকর। এই আয় বলে তুড়ি মারলেই আকাশ থেকে নেমে আসবে।” স্বামীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বঙ্কুর দিকে তাকালেন এবার। “না ভাই বঙ্কু ঠাকুরপো, তাড়াহুড়োর কিছু নেই। তুমি রয়ে সয়ে যা করার করো। ওই নাস্তিকের কথা শুনো না।”
বঙ্কু হাসিমুখে বলল, “আমি সবই ব্যবস্থা করে রেখেছি। আপনারা চা খেয়ে নিন ; তারপরই শুরু করা যাবে।”
আশালতা বললেন, “আমরা কিন্তু আজ খাওয়া দাওয়ার বাদ বিচার করিনি।”
“কোনো বিচারের দরকার নেই। আমি শুধু বলেছিলাম, আসবার সময় পরিষ্কার জামা কাপড় পরে আসবেন। আর পারলে তিনটে করে তুলসীপাতা চিবিয়ে আসবেন।”
“তা এসেছি।”
“তবে আর কি! যখন বসব তখন জুতোটুতো খুলে হাত পা মুখ ধুয়ে নেবেন। তাতেই হবে। বসুন, চায়ের কতটা হল দেখি।”
বঙ্কু চলে গেল। চার জনে বসে বসে বঙ্কুর বাড়ির বাইরের দিকটা দেখতে লাগলেন। বাড়ি ছোট নয় বলেই মনে হচ্ছে। ভেতরের দিকে ঘরটর বেশি থাকতে পারে, কে জানে। বাগানটা ভালই সাজিয়েছে বঙ্কু, দেদার গাছপালা। বাড়ির চারদিকে এত নিম কাঁঠালের গাছ রেখেছে কেন?
কুয়ো থেকে জল তোলার শব্দ হচ্ছিল। অন্ধকার হয়ে গেল।
জগবন্ধু সিগারেট খেতে খেতে রমেশকে বললেন, “ভূতো বঙ্কু এত সব করল কি করে হে রমেশ? দৌলত ভূতে জুগিয়েছে?”
রমেশ বললেন, “ওর তো এখানে কিছু জমি-জায়গা আছে। লোক রেখে চাষবাস করায়। তা ছাড়া কাঠের কারবারও করে সামান্য।”
“এ বাড়িতে থাকে কে কে?”
“বাড়ির কাজকর্ম যারা করে তারাই থাকে—আর কে থাকবে?”
জগবন্ধু ঠাট্টা করে বললেন, “ওর বউ কি প্রেতের ঠেলাতেই চম্পট দিয়েছে হে?”
যামিনী হঠাৎ বললেন, “কিসের যেন গন্ধ আসছে?”
আশালতা চারপাশে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাক টানলেন, তারপর বললেন, “ঘন দুখ উথলে ওঠার মতন, তাই না? পায়েস পায়েস।”
“কেউ কি এলেন নাকি আশেপাশে।”
যামিনী চার দিকে তাকালেন।
আশালতার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। তিনি যামিনীর হাত চেপে ধরলেন।
এমন সময় চা এল। বেতের ট্রেতে সাজানো। বাড়ির কাজের লোক বয়ে এনেছে। পেছনে বঙ্কু।
“কিসের একটা গন্ধ পাচ্ছি, ঠাকুরপো?” যামিনী বললেন।
“গন্ধ!…ও বুঝেছি, আসলি চন্দনের গন্ধ। যে-ঘরে আমরা বসব, সেই ঘরে ধূপ জ্বেলে দেওয়া হয়েছে,” বঙ্কু বলল।
বঙ্কুর আত্মা-সাধনার ঘরখানি দেখার মতন। মাঝারি ঘর, নানা ধরনের আসবাব। গোল টেবিল, হাতলহীন চেয়ার, হ্যাট স্টান্ডের মতন কি একটা একপাশে রাখা, চার কোণে চারটে লোহার খাঁচা। খাঁচার মধ্যে মাটির মালসায় ধুনো দেওয়া হয়েছে। একদিকে একটা চোঙা ঝুলছে—একসময় রেডিওতে যেমন হালকা গোছের চোঙা লাগানো থাকত অনেকটা সেই রকম। কোণের দিকে একটা কুলুঙ্গি কাচ দিয়ে ঢাকা। কাচের আড়ালে টিমটিমে একটা লাল বাতি জ্বলছে। সারা ঘর জোড়া মোটা শতরঞ্জি। পায়ের শব্দ হয় না। হালকা নীল লাইম ওয়াশ করা দেওয়াল, চার দেওয়ালে চারটি কাঠের গুঁড়োভরা মরা বেড়াল আর কাকের দেহ ঝুলছে। কুচকুচে কালো রং বেড়াল দুটোর। জানলা ঘেঁষে একটা সরু টেবিলের ওপর একটা পেটা ঘণ্টা, গোটা দুয়েক শাঁখ, ধূপদানি। জানলাগুলো কালো পরদা দিয়ে ঢাকা।
জুতো খুলে হাত পা ধুয়ে জগবন্ধুরা ঘরে ঢুকেছিলেন। ঘরের মধ্যিখানে গোল টেবিলের চারপাশে চেয়ার সাজানো। বঙ্কু সকলকে বসতে বলল।
টেবিলের ওপর একটা চাকা-লাগানো ছোট তেকোঠ পড়ে ছিল।
জগবন্ধু চোখ সইয়ে নিয়ে বললেন, “এটা কী?”
বঙ্কু বলল, “ওটা লেখার জিনিস। ওর মধ্যে একটা সরু-গর্ত আছে পেনসিল ফিট করার জন্যে। আত্মারা বেশির ভাগ সময় কথা বলতে চান না। তখন মিডিয়াম ওই জিনিসটার ওপর হাত রেখে আত্মার কথাবার্তা লিখতে পারেন।”
“লিখবে কিসে? চাকা লাগানো কেন?”
“কাগজে লিখবে? কাগজ দিয়ে দেব। চাকা লাগানো রয়েছে হাত ভাল সরবে বলে। তাড়াতাড়ি লেখা যাবে।”
জগবন্ধু বললেন, “কলটি তো বেড়ে বানিয়েছ!”
আশালতা বার কয়েক খুক খুক করে কাশলেন। ঘরের চারদিকই বন্ধ। ধূপধুনোর ধোঁয়ায় ঘরের সবই অস্পষ্ট।
রমেশ বললেন, “তা আর দেরি কেন?”
“না, এবার শুরু করব। তার আগে একটা কথা বলে নিই। টর্চ, দেশলাই, লাইটার—কোনো রকম আলো জ্বালবেন না। আমায় দিয়ে দিন।”
জগবন্ধু টর্চ বাইরে রেখে এসেছেন। দেশলাই দিয়ে দিলেন।
বঙ্কু বলল, “ওই লাল বাতিটা দেখছেন? যদি দেখেন বাতিটা খুব দপদপ করছে বুঝবেন আত্মা কাছাকাছি এসে গেছে। এই ঘরে তাঁর আবির্ভাব হলে আলো নিবে যাবে।”
জগবন্ধু বললেন, “আমরা কি লাল আলোর দিকে চেয়ে থাকব?”
“না। আপনারা মুখ নিচু করে চোখ বুজে যাঁকে দেখতে চান, অবশ্য তাঁর মৃত্যু হওয়ার দরকার, তাঁর কথা এক মনে ভাববার চেষ্টা করবেন। সবাই যদি একই লোকের কথা ভাবেন তাতে তাড়াতাড়ি কাজ হতে পারে। কিন্তু তা তো সম্ভব হয় না। চারজনে চাররকম ভাবলে ক্রস লাইন হয়ে যায়।”
“কলকাতার টেলিফোনের মতন?” জগবন্ধু বললেন।
বঙ্কু বলল, “এবার শুরু করা যাক। আপনারা এখন কেউ আলোর দিকে তাকাবেন না। যদি আলো কাঁপে আমি বলে দেব তখন তাকাবেন। আর একটা কথা, আপনাদের ভাগ্য যদি ভাল হয়—আত্মার কথাও শুনতে পাবেন। সূক্ষ্ম আত্মা, গলার স্বর আরও সূক্ষ্ম। কানে শোনা মুশকিল। ওই যে চোঙাটা দেখছেন, ওই চোঙা দিয়ে স্বর শোনবার ব্যবস্থা আমি করেছি। টোনটাকে হাই ভলুম করার ব্যাপার আর কি!”
যামিনী বললেন, “লেখালেখির চেয়ে গলা শোনা ভাল, নয়রে, আশা?”
আশালতার গা ছমছম করছিল। বলল, “কেন, লেখাটা খারাপ?”
রমেশ বললেন, “আমার হাতের লেখা ন্যাস্টি। তোমার তো কাগের বগের ঠ্যাং। যামিনী দিদির আঙুলে বাত। কে লিখবে! জগোবাবু পিঁপড়ে বানান লিখতে তিনটে চন্দরবিন্দু বসায়—ওর কথা বাদ দাও।”
বঙ্কু বলল, “সবই আত্মার ইচ্ছে। তিনি যদি কথা বলতে চান শুনতে পাবেন, যদি লেখাতে চান যার ওপর ভর করবেন তাঁকে লিখতে হবে। আমি নাচার। নিন তৈরি হন। আর কথাবার্তা নয়, ঠিক ঠাক হয়ে বসুন।”
বঙ্কু চারপাশ ঘুরে ফিরে সব একবার দেখে নিল। কোথা থেকে কাগজ বার করে টেবিলের ওপর রাখল। তারপর ঘরে হালকা বাতিটা নিবিয়ে বলল, “রেডি”। বলে পেটা ঘণ্টায় ঢং করে ঘন্টা বাজাল।
অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে বঙ্কু দূরে এক কোণে গিয়ে বসল। কুলুঙ্গির টিমটিমে লাল বাতিটাই শুধু জ্বলতে লাগল।
যামিনী নিজে চোখ বন্ধ করার আগে একবার আড়চোখে দেখে নিলেন জগবন্ধু চোখ বন্ধ করেছেন কি না।
আশালতা ঢোক গিলে চোখ বুজে ফেললেন।
রমেশ মাথা নিচু করল।
বঙ্কু খানিকটা তফাত থেকে এমন একটা উদ্ভট শ্লোক পড়তে লাগল মনে হল যেন লামাদের দেশ থেকে আমদানি করেছে মন্ত্রটা।
বঙ্কুও চুপ করে গেল।
ঘর একেবারে নিস্তব্ধ। কোনো রকম শব্দ নেই। নিশ্বাসের শব্দও যেন শোনা যাচ্ছে না। ধুনোর ধোঁয়ায় ঘর ভরে গিয়েছে, ধূপের ঘন গন্ধ।
বসে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে জগবন্ধু কিছু বলে ফেলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় টেবিলের ওপর রাখা তেকাঠ নড়ে উঠল। যামিনী ফিসফিস করে বললেন, “এসেছেন।”
যিনি এসেছিলেন তাঁর বোধ হয় তেমন পছন্দ হল না জায়গাটা, তেকাঠ নাড়িয়েই চলে গেলেন।
খানিকটা পরে আবার একজন এলেন, তেকাঠ নাচালেন, রমেশের দিকে গড়িয়েও দিলেন তেকাঠ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত অধিষ্ঠান করলেন না। পালালেন।
বার তিনেক এই রকম হল। এক একটি আত্মা আসেন, দু চার মুহূর্ত থাকেন, তারপর চলে যান। আত্মদর্শীরা তাঁদের নাগাল পান না।
শেষে আচমকা বঙ্কু বলল, “বাতি কাঁপছে, কেউ আসছেন। কাছকাছি এসে গেছেন।”
চারজনই কুলুঙ্গির বাতির দিকে তাকালেন। খুব কাঁপছে। মানে আত্মা একেবারে ঘরের দোরে।
যামিনী আঁচলটা গলায় জড়িয়ে দিলেন, আশালতা দু’হাত জোর করে কপালে ঠেকালেন।
লাল বাতি দপ দপ করতে করতে নিবে গেল।
সামান্য চুপচাপ থাকার পর বঙ্কু বলল, “উনি এসেছেন, বউদি! এবার কথাবার্তা বলা যেতে পারে। আপনারা কি কিছু বলবেন?”
বাতি নিবে যাবার পর ঘরে এক ফোঁটাও আলো নেই। ঘুটঘুটে অন্ধকার। যামিনী স্বামীকেও ঠাওর করতে পারছিলেন না, বললেন, “তুমিই কথা বলো, বঙ্কু ঠাকুরপো।”
বঙ্কু বলল, “জগুদা, আপনারা বলবেন কিছু?”
রমেশ বললেন, “না না, তুমিই যা বলার বলো, আমরা শুনতেই চাই।”
বঙ্কু বলল, “বেশ।…কথার মধ্যে আপনারা কিন্তু বাধা দেবেন না।”
দু মুহূর্ত পরে বঙ্কু আগত আত্মার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করল।
বঙ্কু বলল, “আপনি এসেছেন, আমরা বড় খুশি হয়েছি। কোথা থেকে এসেছেন?”
আত্মা জবাব দিলেন, শোনা গেল না।
বঙ্কু বলল, “আপনার কথা কিছু শুনতে পাচ্ছি না। একটু জোরে জোরে বলুন।” চোঙা দিয়ে এবার আওয়াজ বেরুল। মেয়েলি গলা।
“আমাদের সৌভাগ্য আপনি এসেছেন। নমস্কার নিন। কোন স্তর থেকে আসছেন?” বঙ্কু বলল।
“সূক্ষ্ম তিন থেকে।”
“অনেক দূর থেকে আসছেন। বড় কষ্ট হয়েছে আসতে। আপনার পরিচয়?”
“বাড়িতে সবাই তিরি বলে ডাকত, ভাল নাম ছিল রাণী।”
বঙ্কু যেন চমকে উঠল। বলল, “সেকি। দিদি তুমি? তুমি এসেছ? এতদিন কত জনকেই তো ডেকেছি, তুমি তো কোনোদিন আসনি?”
“না। তুই ডাকতিস জানি। ইচ্ছে হত আসতে। তবু আসিনি, আজ এলাম চাঁদের হাট দেখতে।”
“চাঁদের হাট? বুঝেছি, তুমি জগুদা রমাদার কথা বলছ! সঙ্গে বউদিরা রয়েছেন—যামিনী বউদি, আশা বউদি।”
“জানি সব জানি। দিব্যি সব সুখে রয়েছে। তাইতো দেখতে এলাম। একেই বলে কপাল। ওদের সুখের কপাল।”
“সংসারে সুখের কপাল নিয়ে কজন আর আসে, দিদি। তোমার আমার মতন দুঃখের কপালই বেশি।” বঙ্কু ভারী গলায় বলল।
“আমাদেরও সুখ হত রে, বঙ্কু। কতকগুলো পাজি নচ্ছার হতচ্ছাড়ার জন্যে হয়নি। ওই তো জগুদা, ও আমায় বিয়ে করতে পারল না?”
জগবন্ধু খস খসে গলায় একটা আওয়াজ করলেন। যার অর্থ হল, এ-সব কী হচ্ছে?
বঙ্কু বলল, “বিয়ে তো বাপ-মায়ে দেয়, দিদি! জগুদা কি করবে?”
“বিয়ের বেলায় বাপ-মা। আর আমার সঙ্গে যে ছেলেবেলা থেকে প্রণয় ছিল।”
জগবন্ধু আর সামলাতে পারলেন না। বিরক্তির সঙ্গে বললেন, “এটা হচ্ছে কী? তামাশা?”
তিরির আত্মা বলল, “তামাশা কে করেছে, তুমি না আমি?”
“বাজে বোকো না, আমি তোমার সঙ্গে প্র—প্রণয় করিনি।”
‘আহা রে! করিনি—মাইরি আর কি! ছেলেবেলায় কে আমায় পুকুরে নামিয়ে সাঁতার শেখাত, বাগানে নিয়ে গিয়ে অখাদ্য কুখাদ্য খাওয়াত! বলুক না ওই রমাদা। সে তো দেখেছে নিজের চোখে।”
জগবন্ধু গলা চড়িয়ে বললেন, “ছেলেবেলার কথা বাদ দাও। তখন সবাই নাবালক। একসঙ্গে মিলেমিশে খেলাধুলো করে, গাছের আম পাড়ে, কোষ্ট কুল খায়, কানামাছি খেলে। ওকে কেউ প্রণয় বলে না।”
তিরি বলল, “তাই নাকি! তা পনেরো বছর পেরিয়ে গেলে তখনও কি ছেলেবেলা থাকে?”
“পনেরো পেরিয়ে তুমি বড় পাকা হয়ে গিয়েছিলে।”
“তোমার হাতে পড়লে পাকা হব না। কাঁচা আতা চালের তলায় গুঁজে রেখে মা মাসিরা আতা পাকাত দেখেছি। আর দেখলাম তোমাকে—। আমার কাঁচা বয়েসটাকে কেমন করে পাকিয়ে দিলে।”
রমেশ এই সময় গুন গুন করে টপ্পা গেয়ে উঠল, “আমার কাঁচা পিরীত পাড়ার ছোঁড়া পাকিয়ে দিল গো।”
জগবন্ধু ধমক মেরে বললেন, “ভালগার। বেহায়াপনা। আত্মা এমন বেহায়া হয় জানতাম না। ছ্যা ছ্যা—।”
তিরি হি হি করে হেসে বেঁকা গলায় বলল, “কেন গো জগুদা, ছ্যা—ছ্যা কেন? আমার সেই কচি বয়েসে যখন বাতাবিতলায় দাঁড় করিয়ে বিল্বমঙ্গল প্লে করতে তখন তোমার বেহায়াপনা কোথায় যেত!”
“বিল্বমঙ্গল ঠাকুর-দেবতার ব্যাপার! তুমি তখনও মুখ্যু ছিলে এখনও মুখ্যু।”
তিরি ইস ইস শব্দ করল জিবে। বলল, “মুখ্যু তো বটেই নয়ত আমাকে পড়া দেখিয়ে দেবে বলে কেনই বা তেতলার ছাদে নিয়ে যাবে বলো। আহা দুজনে কত পড়াই পড়তাম—পড়তে পড়তে মুচ্ছো যেতাম। আমি রোগা পাতলা—তাই না তিরতিরে তিরি। আর তুমি গোবা গবলা। তোমার মুচ্ছো হলে সে ভার কি সইতে পারি, হেলে যেতাম।”
জগবন্ধু টেবিল চাপড়ে বললেন, “এ-সব হচ্ছে কি? আমার কাছা ধরে টান মারা হচ্ছে?”
যামিনী তিরির উদ্দেশে বললেন, “দাও ভাই দাও বুড়োর কাঁচাকাছা খুলে ন্যাংটো করে দাও।”
তিরি উৎসাহ পেয়ে বলল, “ও-হাঁড়ি কি ভাঙা যায়, বউদি। ও হল জ্বালা। বলতে গেলে সাত কাহন। আমার অত সময় নেই। অনেকক্ষণ এসেছি। যাবার সময় হয়ে গেল।”
জগবন্ধু গজরাতে লাগলেন, “মানুষ মরে গিয়েও এত মিথ্যে কথা বলতে পারে।”
তিরি ফোঁস করে উঠল। “কোপচো না। জ্যান্ত থাকতে তুমি আমায় দিয়ে মিথ্যে কথা বলিয়েছ? না নিজে বলছ? লজ্জা করে না। ঠাকুমার সত্যনারায়ণের মানত করা টাকা চুরি করে এনে দিয়েছি, কিনা জগুদা আমার ঝরিয়াতে সার্কাস দেখতে যাবে। দিইনি? নেমকহারাম একেই বলে! আমার কোলে লম্বা হয়ে শুয়ে উনি বললেন, তিরি আমি তোমার লখিন্দর—তুমি আমার বেহুলা, আমি তোমার প্রেমে মরেছি। তুমি আমায় যমের হাত থেকে উদ্ধার করো। আর তুমি যদি উদ্ধার না করো আমি সংসার ত্যাগ করে ভোলানাথ হয়ে ঘুরে বেড়াব হরিদ্বার লছমনঝোলা। ঠিক এই সময় জ্যাঠামশাই—জগুদার বাবা দরজায় এসে দাঁড়ালেন। আর লখিন্দর আমার গালে ঠাস করে চড় কষিয়ে সাক্ষাৎ যমের পাশ দিয়ে ছুটে পালাল।”
জগবন্ধু চিৎকার করে বললেন, “তোমার সেই ধেষ্টামির জন্যে বাবা আমায় সটান হেতমপুর কলেজে পড়তে পাঠিয়ে দিল তা জান?”
“তা জানব না। আমি তো তখন কুচি খুকি নই। সতেরো বছর বয়েস হয়ে গেছে।—ওই কীর্তির পরও বাড়ি এলে তোমার কত আদিখ্যেতা। আমার এ-গালে চুমু ও-গালে চুমু। এক একদিন গাল আমার নীল হয়ে যেত।”
জগবন্ধু আর্তনাদ করে উঠলেন। “প্রিভিলেজ অফ কিসিং আমার ছিল যে তোমার গালে চুমু খাব?”
“খেয়েছ!”
রমেশ বলল, “তিরি মিথ্যে বলছে না। আমি একদিন জগোবাবুকে কিস করতে দেখেছি। গোয়াল ঘরের পাশে কৃষ্ণচূড়া গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে করছিল।”
জগবন্ধু খেপে গিয়ে বললেন, “ও শালা, আমি হলাম চোর, আর তুমি সাধু!”।
তিরি বলল, “সাধু আবার কোথায়! সেদিন জগুদা একটা গালে চুমু খেয়ে চলে যাবার পর রমাদা এসে বলল, আমি তোদের চুমোচুমি দেখেছি। দে, আমায় দুটো দে, নয়ত বলে দেব বাড়িতে।”
রমেশ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বার কয়েক ঢোঁক গিলল। আমতা আমতা করে বলল, “আমার মনে নেই।”
আশালতা নিচু গলায় বলল, “কী ঘেন্না, কী ঘেন্না! এঁটো মুখে মুখ ঠেকাতে ঘেন্নাও করল না।”
বঙ্কু এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। এবার বলল, “দিদি, তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। তুমি আর কথা বোলো না, হাঁপাচ্ছ।”
তিরি একটু চুপ করে থেকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল। বলল, “সত্যি অনেক দেরি করে ফেললাম। অনেক দূর যেতে হবে। আমি এবার যাই। আমার কর্তা তো হাঁ করে চেয়ে আছেন। তা একটা কথা বলি জগুদা, বিয়ের পর আমার বর কিন্তু একদিনের জন্যেও কাছ ছাড়া করেনি। বড্ড ভালবাসত। কিন্তু কপাল যার মন্দ তাকে কে বাঁচাবে। শখ করে দু ঘটি বুনো সিদ্ধির সরবত খেয়েছিল, তার সঙ্গে চার ছটা কুলপি। ওতেই কাল হল। রাত আর কাটল না। তিরি জপতে জপতে চলে গেল মানুষটা। আর আমিই বা বেজোড়ে থাকি কেমন করে বলো। চার মাসের মাথায় আফিং খেলাম। এখন দুজনে দিব্যি জোড়ে আছি।”
যামিনী শাড়ির আঁচলে চোখ মুছলেন। “আহারে সতী লক্ষ্মী!”
তিরি বলল, “এবার আসি। কথায় কথায় কত রাত হয়ে গেল। চলি গো জগুদা রমাদা। আসি ভাই বউদিরা। তোমরা ভাই সুখে শান্তিতে থাকো। বঙ্কু, আসি ভাই।”
সামান্য চুপচাপ। তারপর বঙ্কু বলল, “দিদি চলে গেছে। লাল বাতিটা আবার জ্বলে উঠেছে। এবার আমাদের উঠতে হবে।”
জগবন্ধুরা চলে যাচ্ছেন, বঙ্কু ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসেছিল।
ফটকের বাইরে এসে জগবন্ধু রাগে গর-গর করতে করতে বঙ্কুকে বললেন, “তুমি একটা হাড় হারামজাদা। শালা চিট!”
যামিনী কয়েদি ধরে নিয়ে যাবার মতন করে জগবন্ধুর ডান হাতটা খপ করে ধরে নিয়ে টান মারলেন। তাঁর বাঁ হাতে ছ শেলের ভারী টর্চ। বললেন, “কে কী সেটা পরে দেখব। আগে বাড়ি চলো।”
দু পা পেছনে রমেশ। আশালতা স্বামীকে হাতখানেক তফাত রেখে হাঁটছেন। আর বার বার স্বামীর মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। মানুষটার ঘেন্নাপিত্তি এত কম! নাক সিঁটকে উঠল আশালতার।
জগবন্ধুরা সামান্য এগিয়ে যেতেই বঙ্কু ফটক বন্ধ করে বাড়ির দিকে ফিরল।
বারান্দায় ওঠার আগেই বঙ্কু খিলখিল হাসি শুনল।
“এত হাসি কিসের?” বঙ্কু বারান্দায় উঠে বলল।
হাসিতে তখন লুটোপুটি খাচ্ছে বঙ্কুর শালী বিজলী। শাড়ি সামলাতে সামলাতে বিজলী বলল, “দিলেন তো সুখের সংসারে আগুন জ্বালিয়ে?”
বঙ্কু হাসতে হাসতে বলল, “দাউ দাউ করে জ্বলবে না রে ভাই ধিকি ধিকি জ্বলবে। ভাগ্যিস তুই টাইমলি এসে পড়েছিলি! বেশ জমল।”
“আমি ভাবছিলুম সাক্ষাৎ জ্যান্ত গলা ধরা না পড়ে যাই।”
“জগুদা তখন নিজেই ধরা পড়ছে, গলা ধরার হুঁশ আছে নাকি তার। নে চল, খিদে পেয়ে গেছে। রাত হল।”
ঘরের মধ্যে পা বাড়াতে বাড়াতে বিজলী বলল, “কাল কিন্তু আমি ফিরে যাব।”
“বেশ তো যাবি। তোকে কে আটকাচ্ছে।”
বিজলী বঙ্কুর গায়ে ঠেলা মেরে বলল, “আহা! কে আটকাচ্ছে!”
কালিদাস ও কেমিস্ট্রি
যেন বাঘে তাড়া করেছে, মহেশ্বরী পড়িমরি করে ছুটে এসে ঘরের মধ্যে আছড়ে পড়ল।
ঘরের মধ্যে তখন সাত আটটা মেয়ে মিলে তালে তালে তালি বাজাচ্ছে, মুখের মধ্যে জিবের শব্দ করছে টক্ টক্ টাকাস্ট্টক্। আশা মেঝেতে উবু হয়ে বসে সিগারেটের কৌটোর মধ্যে রাখা ক্যারামের গুটি বাজাচ্ছিল। আর বকুল হাঁটু থেকে গলা পর্যন্ত পাকে পাকে শাড়িটা জড়িয়ে দুহাত মাথার ওপর তুলে তুড়ি দিয়ে ভ্রূভঙ্গি ও কটাক্ষসহযোগে পা ঠুকে ঠুকে বিচিত্র নাচ নাচছিল। ইরানি নাচ হয়ত। তার গলা হাঁসের গলার মতন দোল খাচ্ছিল।
এই নৃত্যবাদ্যের মধ্যেই মহেশ্বরী একটু আগে উঠে কলঘরে গিয়েছিল। ফেরার সময় বাঘের তাড়া খাওয়ার মতন ছুটতে ছুটতে এসে ঘরের মধ্যে আছড়ে পড়ল। মেয়েরা ভেবেছিল, দৌড়ে আসতে গিয়ে মহেশ্বরী চৌকাটে হোঁচট খেয়েছে। পড়ল তো পড়ল একেবারে আশার ঘাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মহেশ্বরী। আশা মোটাসোটা গোলগাল মানুষ, ব্যাঙের মতন হাত পা তুলে মেঝেতে উলটে গেল। কোনও রকমে মহেশ্বরী শুধু বলল, ‘কার্বন ডায়োক্সাইড আতি হ্যায় রে।’
মুহুর্তের মধ্যে ঘরের চেহারা পালটে গেল। এ-বিছানা ও-বিছানা থেকে মেয়েরা আতঙ্কের ডাক ছেড়ে লাফ মেরে উঠে দরজার দিকে ছুটল, ঊষা ছুটে গিয়ে আলনার পাশে শাড়ি শায়ার আড়ালে লুকোল।
পালাবার পথ পাওয়া গেল না। খোলা দরজা দিয়ে দেখা গেল কার্বন ডায়োক্সাইড আসছে। মেয়েরা তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।
মেয়েরা বলে ‘কার্বন ডায়োক্সাইড’ আসলে নাম ওর ফুলরেণু সোম। কলেজের কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের লেকচারার। এদিকে আবার মেয়ে হোস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্ট।
ঘরের চৌকাটের সামনে দাঁড়িয়ে ফুলরেণু রঙ্গমঞ্চের অবস্থাটা কিছুক্ষণ দেখল; গুটি ছয় সাত মেয়ে, ঘরের মধ্যে তিনটি বিছানাই লণ্ডভণ্ড ধামসানো। মেয়েরা বিছানার কাছে, কেউ বা দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের জানলা খোলা, পড়ার টেবিলে কেরোসিন টেবিল-বাতি জ্বলছে। বকুল তার হাত দুটো মাথার ওপর থেকে নামিয়ে নিয়েছিল, কিন্তু সারা অঙ্গে পাকে পাকে জড়ানো শাড়িটা আর আলগা করতে পারেনি; তাকে লেত্তি পরানো ঘোড়া লাট্টর মতো দেখাচ্ছিল।
চৌকাটে দাঁড়িয়ে ফুলরেণু বলল, “এত নাচগান হল্লা কিসের?”
মেয়েদের মুখে কথা নেই, ঠোঁটে সেলাই দিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে। একেবারে নিরীহ, গোবেচারি মূর্তি সব।
অপরাধীর মতন মুখ করে বকুল শেষে বলল, “আমরা একটু আনন্দ করছিলাম দিদি।”
আনন্দ করার কথায় ফুলরেণু বিন্দুমাত্র আনন্দিত হল না; বরং আরও গম্ভীর বিরক্ত মুখ করে বলল, “আনন্দ করতে হলে মাঠে যাও, রাস্তায় যাও, আমার হোস্টেলের বাইরে যাও। এখানে আনন্দটানন্দ চলবে না। এটা আনন্দধাম নয়। এরকম বেয়াড়াপনা, হইহুল্লোড় আমি অ্যালাও করব না।” ফুলরেণু থামল, যেন তার রায় দিয়ে দিল দু-কথায়। তারপর মেয়েদের জনে জনে লক্ষ্য করল, বকুলকেও। বলল, “বকুল তুমি ওটা কি করে শাড়ি পরেছ? ওটা শাড়ি, না সাপের খোলস। আমার এখানে সাপের খোলস করে শাড়ি পরা চলবে না। যত অসভ্যতা, সব…প্রীতি, তুমি আড় চোখে চোখে কী বলছ? আমি তোমাদের এ সব আড়বাঁশি-চাউনি দু চক্ষে দেখতে পারি না।…আর, মহেশ্বরী, তুমি—তুমি আমায় দেখে দুদ্দাড় দৌড় দিলে, ভাবলে আমি তোমায় দেখিনি। এভাবে দৌড়তে হলে তোমায় ঘোড়দৌড় মাঠে যেতে হবে, এখানে চলবে না। মেয়েদের কাছে আমি সভ্যতা ভদ্রতা ডিসেন্সি চাই—অসভ্যতা বেলেল্লাপনা নয়।”
আশা ঢোঁক গিলে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, ফুলরেণু ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়ে বলল, “কলেজে তোমরা যা করো আমি দেখে অবাক হয়ে যাই। এ কলেজে ছেলেমেয়ে বলে আলাদা কিছু নেই, তোমরা দল করে সাইকেল চড়ছ, জল ছোঁড়াছুঁড়ি করছ, ছেলেদের সঙ্গে তুই-তুকারি করছ, ডালমুট কেড়ে খাচ্ছ! কী যে না করছ।…এ কলেজে কোনও ডিসিপ্লিন নেই, সহবত শিক্ষা, ভালমন্দ, ছোটবড় জ্ঞান দেখি না কোথাও; সবাই যেন নাগরদোলায় চড়ে আছে। কী অসভ্য সব। ছি ছি!…তা আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি নাচানাচি, লাফালাফি, তুড়ি বাজানো, যা তোমাদের ইচ্ছে তোমরা কলেজে সেরে আসবে, আমার এখানে আমি অসভ্যতা করতে দেব না।…যাও, নিজের নিজের ঘরে যাও।…মহেশ্বরী, আমি আধঘন্টার মধ্যে তোমাদের ঘর পরিষ্কার পরিছন্ন দেখতে চাই।” ফুলরেণু শেষবারের মতন তার তাড়না শেষ করে যেমনভাবে এসেছিল, সেইভাবেই চলে গেল! বারান্দায় তার পায়ের শব্দ শোনা গেল কয়েক মুহূর্ত।
ফুলরেণু অদৃশ্য হলে মেয়েরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। আলনার আড়াল থেকে ঊষা বেরিয়ে এল, তার চুলের বিনুনিতে কার যেন নীচের জামার হুক আটকে ঝুলছে।
মহেশ্বরী বলল, “বাস রে বাস, কার্বন ডায়োগাইড কি টেমপারেচার হট হয়ে গেছে রে…”। মহেশ্বরীর হিন্দি-বাংলা মাঝে মাঝে এই রকমই হয়। যদিও সে বাংলা কথা মোটামুটি ভালই বলতে পারে বলে তার ধারণা।
প্রীতি বলল, “হবে না। কতদিন ধরে বলছি জামাইবাবুর সঙ্গে দিদির একটা হট-লাইন পেতে দে, তা তো তোরা দিবি না।”
বকুল পাক দেওয়া শাড়ির প্যাঁচ গা থেকে খুলতে খুলতে বলল, “বলিস না আর তোরা। হট-লাইন না পাততেই এত হট, পাতলে সারাদিন আগুন জ্বলবে।”
মেয়েরা সমস্বরে খিলখিল করে হেসে উঠল।
আসর ভেঙে যেতে ঊষা বলল, “এই বা কি কম জ্বলছে। একেবারে কোপানল। আজ আবার জামাইবাবু পড়াতে আসবে। দিদি কী করবে ভাই? মদনভস্ম।”
মেয়েরা এবার কলকল করে হাসল।
এই গল্পের এইটুকু ভূমিকা। কিন্তু ফুলরেণুর রাগ বা উষ্মা কিংবা বিরক্তি বুঝতে হলে আমাদের এবার তার কাছে যেতে হবে।
মেয়েদের শাসন করে ফুলরেণু তার ঘরে ফিরে গেল। ঘরে ঢুকল না ঠিক, পশ্চিমের দিকে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। সন্ধে হয়ে গেছে। সামনের নেড়া জমিতে ধুলোভরা করবী ঝোপ। ফাল্গুনের বাতাসে মাঝে মাঝে দুলছিল। হোস্টেলের পাঁচিলের ওপাশে রাস্তা, টাঙা গাড়ি যাচ্ছিল, মাঝে মাঝে দু একটা লরিটরি। শীত কবে ফুরিয়ে গেছে, সামনে ফাগুয়া, রানি-বাঁধের দিক থেকে ধোপাপট্টির হল্লা ভেসে আসতে শুরু করেছিল, ফাগুয়ার গান হচ্ছে। বাতাস খুব এলোমেলো, দক্ষিণ থেকে দমকে দমকে আসছে আর যাচ্ছে। অনেকটা তফাতে দেশবন্ধু সিনেমা হল, এখন আর গান নেই, ন’টা নাগাদ আবার সিনেমা হলের লাউডস্পিকারে গান বাজাবে এবং সেই তীব্র গান এখানেও ভেসে আসবে। ফুলরেণুর পক্ষে তখন আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়।
বাইরে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফুলরেণু ঘরে এল। এসে আবার জল খেল এক গ্লাস। এই নিয়ে আধঘণ্টার মধ্যে তার তিনবার তিন গ্লাস জল খাওয়া হল। না, এখনও এতটা গরম পড়েনি যে ক্ষণে ক্ষণে জল খেতে হবে। তবু ফুলরেণুকে আজ জল খেতে হচ্ছে। মাথা আজ আগুন, ফুলরেণু ভাবতেও পারছে না, এটা কী করে হয়, কী করে হওয়া সম্ভব? ছি ছি!
ঘরের মধ্যে নড়ে চড়ে ফুলরেণু বিছানায় গিয়ে বসল, বসে আবার উঠল, টেবিলের দিকে তার আর তাকাতে ইচ্ছে করছিল না। একরাশ খাতা টেবিলের এক পাশে ডাঁই করে পড়ে আছে। কয়েকটা মাত্র দেখা হয়েছে, বাকিগুলো হয়নি। কে বিশ্বাস করবে, নিরীহ ওই খাতাগুলোর মধ্যে এ-রকম বেলেল্লাপনা লুকিয়ে থাকতে পারে! ছি ছি। ফুলরেণুর হাতের আঙুলের ডগা বোধহয় এখনও ঠাণ্ডা হয়ে আছে ঘামে। বুকের ধকধক ভাবটা কমেছে অবশ্য, মাথা এখনও বেশ গরম, কপালের শিরা দপদপ করছে। ফুলরেণু টেবিলের দিকে যেন লজ্জায় আর তাকাতে পারছিল না। মনে হচ্ছিল: মৃদুলা যেন বুকের কোথাও একটু আবরণ রাখেনি, একেবারে বেহায়ার মতন বসে আছে, বসে বসে নিজেকে দেখাচ্ছে। ছি ছি! ওই একরত্তি মেয়ে পড়ে তো সেকেন্ড ইয়ারে, কতই বা বয়স উনিশ কুড়ি বড়জোর না হয় একুশ, এরই মধ্যে এত! অসভ্য, পাকা মেয়ে কোথাকার।
বিছানায় স্থির হয়ে বসে থাকতে পারল না ফুলরেণু, উঠল; উঠে জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াল দু দণ্ড। সেকেন্ড ইয়ারের ছেলেমেয়েদের ক্লাসে একটা প্রশ্নের উত্তর লিখতে সে দিয়েছিল। একেবারে সাধাসিধে প্রশ্ন: হোয়াট আর দি চিফ প্রপারটিস অফ সালফার ডায়োক্সাইড? হাউ ইজ ইট প্রিপেয়ারড, অ্যান্ড ফর হোয়াট পারপাসেস ইজ ইট ইউসড?…এই প্রশ্নের উত্তর যা লিখেছে মৃদুলা তাতে তাকে শক্ত হাতে নম্বর দিলেও দশের মধ্যে অন্তত চার দিতে হয়। অবশ্য এ পরীক্ষা নম্বর দেওয়া-দেওয়ির নয়, ছেলেমেয়েদের কিছু আসে যায় না এতে। ফুলরেণু নিজে ফাঁকিটাকি পছন্দ করে না, পড়ানোর ব্যাপারে সে খুব কড়াকড়ি করে, নিজে পরিশ্রমী; ছেলেমেয়েরা কেমন পড়ছে, কতটা শিখছে তা তার দেখা দরকার—এই বিবেচনায় নিজের ক্লাসে মাঝে মাঝে ‘লেসন টেস্ট’ নেয়। তার জন্য আলাদা খাতা করতে হয়েছে ছেলেমেয়েদের। ফুলরেণু ঘাড়ে করে সেই খাতা বয়ে আনে, দেখে, আবার ক্লাসে ফেরত দেয়। এবারে গতকাল তার সেকেন্ড ইয়ারের কেমিস্ট্রি ক্লাসে ওই প্রশ্নটা লিখতে দিয়েছিল; প্রপারটিস অফ সালফার ডায়োক্সাইড…।
ফুলরেণু জানলার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে টেবিলের দিকে আবার একবার তাকাল। যেন আড়চোখে মুদুলাকেই দেখছে। ‘মৃদুলা তুমি সালফার ডায়োক্সাইডের চিফ প্রপারটিস যা লিখেছ—ডিসইনফেকটান্ট, ব্লিচিং অফ কালারড মেটিরিয়াল…এ সব মোটামুটি ঠিক, কিন্তু তোমার খাতার মধ্যে ওটা কি?’ ফুলরেণুর চোখের দৃষ্টি যেন এই কথাগুলো বলল। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের দিকে আর সে তাকাতে পারল না, কানের লতি গরম হয়ে উঠল; মুখ ফিরিয়ে নিল।
জানলার কাছে আরও একটু দাঁড়িয়ে থেকে ফুলরেণু বিছানায় এল, বসল। চশমার কাচটা মুছে আবার পরল। গালে হাত রেখে ভাবল খানিকটা। তারপর উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। লবঙ্গ খাবার ইচ্ছে করছিল, মুখ শুকিয়ে যাচ্ছে বার বার। জিবে আর কোনও স্বাদ পাওয়া যাচ্ছে না। অগত্যা ফুলরেণুকে টেবিলের কাছে এসে লবঙ্গের শিশি বের করতে হল।
লবঙ্গ মুখে দিয়ে নিতান্ত যেন জোর করেই ফুলরেণু চেয়ারে বসল। বসে তাকাল: টেবিলের ওপর মৃদুলার খোলা খাতা; পাশে পেপারওয়েট চাপা দেওয়া ভাঁজ করা চিঠি। এই খোলা চিঠিটাই মৃদুলার খাতার মধ্যে পাওয়া গেছে। যদি খামের মধ্যে থাকত ফুলরেণু দেখত না। একেবারে খোলাখুলি, তায় আবার রঙিন ফিনফিনে কাগজ। চোখে না পড়ে পারেনি।
কাঠি দিয়ে বাচ্চারা যেমন শুঁয়োপোকা ছোঁয়, ফুলরেণু অনেকটা সেইভাবে তার খাতা-দেখা লাল-নীল পেন্সিল দিয়ে চিঠিটা ছুঁল। এখনও তার গা বেশ সিরসির করছে। মুখের মধ্যে জিবে লবঙ্গের ঝাল ভাবটায় ঠোঁট ভিজে গিয়েছিল, লালা আসছিল সামান্য।
মৃদুলা যে চূড়ান্ত অসভ্য হয়ে গেছে, ফুলরেণুর তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হচ্ছিল না। মেয়ে একেবারে পেকে হলুদ। লজ্জা-শরম বলে কিছু নেই। ছি ছি ওইটুকু মেয়ে, এই বয়সে এতটা উচ্ছন্নে গেছে কে জানত! বুদ্ধিসুদ্ধি তো একেবারে কম নেই, কিন্তু এই তোমার রুচি? আড়াই পাতা ধরে ভালবাসার চিঠি লিখেছ। তুমি এত শয়তান যে কাকে চিঠি লিখছ তা কোথাও ধরাছোঁয়ার উপায় নেই, নীচে নিজের নামটাও লেখনি। তা বলে হাতের লেখাটা যে তোমার তা তো বোঝাই যায়, খাতার আগে পেছনে তোমার বাংলা হাতের লেখার নমুনা আছে।…পেটে পেটে এত শয়তানি তোমার, অথচ মুখ দেখে বোঝার উপায় নেই।
হতচ্ছাড়া পাজি মেয়ে কোথাকার। তুমি এত ধূর্ত যে কাকে চিঠিটা লিখেছ বুঝতে পারছি না। কলেজের কোনও ছেলেকে নিশ্চয়। তার নাম জানতে পারলে দেখতুম। এই কলেজে তাকে আর ঢুকতে দিতাম না। প্রিন্সিপ্যালকে বলে তাড়িয়ে দিতাম। তোমাকেও। তোমাদের শাস্তি এবং শিক্ষা হওয়া দরকার।
কিন্তু—ফুলরেণু ভেবে দেখল, এ যা কলেজ এখানে কোনও কিছুরই শাস্তি হত না, শিক্ষাও নয়। ছেলেমেয়েরা এইরকমই, কোনও সহবত শেখে না, মানে না। বিশ বছরের ধুমসি মেয়ে দুটো ছোঁড়ার সঙ্গে সেদিন কলেজ-মাঠে সাইকেল রেস দিচ্ছিল। আর একদিন এক ডজন কলা কিনে এনে থার্ড ইয়ারের ছেলেমেয়ের মধ্যে সে কি লুফোলুফি, কলা ছোড়াছুড়ি, খামচাখামচি। ক্লাসে কোনও ছেলে জব্দ হলে মেয়েগুলো উলু দেওয়ার মতন শব্দ করে ওঠে, মেয়েরা জব্দ হলে ছেলেরা টেবিল চাপড়ে গরুবাছুরের ডাক ডাকে। এত হুড়োহুড়ি দাপাদাপি, নাচানাচি, ঝগড়াঝাটি, তুই-তোকারি ছেলেমেয়েদের মধ্যে, তবু প্রফেসাররা কেউ কোনও কথা বলে না। বরং দীপনারায়ণ জুবিলি কলেজের যেন এটাই ঐতিহ্য। তেমনি হয়েছেন প্রিন্সিপ্যাল, বুড়ো মানুষ, ছেলেমেয়েদের হাতেই লাগাম তুলে দিয়েছেন, যা করার তোমরা করো, কেউ রাশ ধরবে না।
এ-রকম যদি কলেজ হয় তবে ছেলেমেয়েরা এর বেশি কী হবে? প্রফেসারদেরও কাণ্ডজ্ঞান বলে কিছু নেই; নিতান্ত তারা মাস্টার-মাস্টারনি, বয়স হয়েছে, চুলটুল পেকেছে, কারও কারও দাঁত পড়েছে, মেয়েদেরও কারও কারও গায়ে গতরে মেদ জমে মাথার চুল উঠে ভারিক্কি হয়েছে—নয়ত এরাও সব এই কলেজের ছেলেমেয়েদের মতন, বাঁধাবাঁধি ধরাধরি বলে কিছু নেই। নিজেদের ঘরে বসে রঙ্গ রসিকতা, হাহা হোহো দাদা-দিদি করে দিব্যি আছে সব। প্রফেসারস রুমের একটা পাশে পার্টিশান করা মেয়ে প্রফেসারদের ঘর। কিন্তু সারা দিনে যদি একটা ঘন্টাও সেই ঘরে মেয়ে প্রফেসাররা বসে! তারা প্রায় সব সময়ই পুরুষদের ঘরে বসে গল্প করছে, চা শরবত খাচ্ছে, পান চিবুচ্ছে, জদা বিলি করছে। ফুলরেণু অনেকবার এ-বিষয়টা আভাসে ইঙ্গিতে বলতে গেছে মেয়েদের। কথাটা কেউ কানে তো তোলেনি; যেন শোনার মতন বা ভাববার মতন কথাই ওটা নয়। ফুলরেণু এ কলেজে নতুন, মাত্র মাস ছয়েক এসেছে; তার পক্ষে পাঁচ সাত এমন কি দশ বছরের পুরনো মেয়ে প্রফেসারদের আর কি বা বলা সম্ভব। হিস্ট্রির সুমিত্রা দেবী তো একদিন বলেই দিয়েছিলেন, “এ সব ফিকির ভাল না, বহিন। ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি ছোড় দো।” হাসতে হাসতেই বলেছিলেন সুমিত্রা দেবী, কিন্তু খোঁচাটা বেশ লেগেছিল ফুলরেণুর। বেহারি মেয়ে সুমিত্রা দেবী, সাত বছর এই কলেজে আছেন, এখানকারই মেয়ে, স্বামী ছেলেদের স্কুলের হেডমাস্টার। দীপনারায়ণ জুবিলি কলেজের ধারাবাহিক ইতিহাস তাঁর মুখে ম্যাগনাকার্টা চার্টারের মতন, রাজা দীপনারায়ণের কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, আদর্শ তাঁর মুখস্থ। এক দুই তিন করে পর পর তিনি বলে দিতে পারেন; এখানে নারী পুরুষের ভেদাভেদ নেই, জাতিধর্ম সংস্কার নেই, প্রাদেশিকতা নেই, মাস্টার-মাস্টারনির দাপট নেই…ইত্যাদি। সোজা কথা, দীপনারায়ণ জুবিলি কলেজেরর প্রফেসাররাও এই কলেজের গড়িয়ে যাওয়া জলে গা ডুবিয়ে মহাসুখে দিন কাটাচ্ছেন।
ফুলরেণুর এসব ভাল লাগে না। লাগছেও না। সভ্যতা, ভদ্রতা, সহবত, শিষ্টতা—এ-সব যদি না শেখানো হয় তবে ছেলেমেয়ের মাথা চিবিয়ে খাওয়া ছাড়া আর কিছু হবে না। হচ্ছেও তাই। এই যেমন মৃদুলার বেলায় দেখা গেল। আগে আরও কিছু কিছু দেখেছে ফুলরেণু কিন্তু এরকম পরিষ্কার ও প্রত্যক্ষ নয়, এভাবে হাতেনাতে তার কাছে আর কেউ আগে ধরা পড়েনি।
হাতের পেনসিল টেবিলে ফেলে রেখে এবার আস্তে হাত বাড়াল ফুলরেণু, যেন শুঁয়োপোকার কাঁটা তার হাতে ফুটবে কিনা বুঝতে পারছে না। দু আঙুলে চিঠিটার কোনা ধরে টানল আস্তে আস্তে; বোধহয় কাঁটা যা ফোটার আগেই ফুটেছে, নতুন করে কিছু ফুটল না। চিঠিটা খুলল ফুলরেণু। আবার পড়ল। এই নিয়ে সাত আটবার পড়া হল।
বাব্বা, কী ছটা ভাষার! এতটুকু লাজ-লজ্জা নেই। কিছুই যেন আটকাচ্ছে না। আবার কথায় কথায় কবিতা, ময়ূরের মতন হৃদয় জাগছে, প্রজাপতির পাখার মতন স্বপ্ন ছুটছে, ডালে ডালে ফুল ফুটছে, মাঝরাতে বালিশের কানে কানে কথা হচ্ছে! বালিশের আবার কান! ফুলরেণুর মনে হচ্ছিল মৃদুলাকে কাছে পেলে ঠাস করে এক চড় মারত। কুমারী মেয়ে তুমি, রাত্তিরে বালিশটাকে তুমি অন্য জিনিস ভেবে গাল ঘষছ? স্বভাব-চরিত্র একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে তোমার…ছিছি এ-সব কথা কি ভাবা যায় যে মেয়েমানুষে লেখে। কোনও মেয়ে কি ভাবতে পারে তার বুকের সামনে একটা পুরুষ আয়না ধরুক, ধরে দেখুক কে আছে! অথচ ওই মেয়ে লিখেছে। হতভাগা মেয়ে কোথাকার। আবার কত আশা, আমার সকল কাঁটা ধন্য করে ফুটবে গো ফুল ফুটবে।
চিঠিটা বন্ধ করে ফেলল ফুলরেণু। চোখের পাতাও বুজে ফেলল। দাঁত চেপে চেপে বলল, তোমার ফুল আমি ফোটাচ্ছি ডেঁপো মেয়ে। কাল প্রিন্সিপ্যালের কাছে যাব। তোমার মা বাবার কাছেও যদি যেতে হয় তাও যাব।
চিঠি রেখে দিল ঠেলে ফুলরেণু। এত ভাষার ছটা এরা কোথায় পাচ্ছে এবার যেন তা আবিষ্কার করতে পারল। নির্ঘাত ওই বাংলা-সংস্কৃতের ভদ্রলোক স্বর্ণকমলবাবুর বিদ্যে থেকে। অমন অসভ্য তো আর দেখা যাবে না ভূ-ভারতে। কোঁচা দুলিয়ে ধুলো ঝাঁট দিতে দিতে কলেজে আসছে, মাথায় উড়ু উড়ু চুল, চোখে কুচকুচে কালো ফ্রেমের চশমা, গায়ে ঢিলে পাঞ্জাবি! হাতে চটি চটি বই, কাব্যটাব্যর হবে হয়ত। গলা কী, যেন সব সময় থিয়েটার করছে ক্লাসে। রসিকতায় প্রোফেসাররা মুগ্ধ, ছেলেমেয়েরা সব ইয়ার-বন্ধু হয়ে উঠেছে। ক্লাসে যখন পড়ায় নিজের মানসম্মান সম্রম সৌজন্যটুকু পর্যন্ত রাখে না। কি সব কথা বলে রঙ্গ রসিকতা করে, আজেবাজে গল্প…। ভীষণ ডিস্টার্বিং। ফুলরেণুকে সপ্তাহে অন্তত পাঁচবার ওই কার্তিক-টাইপের লোকটার পাশাপাশি ঘরে ক্লাস নিতে হয়। ছাই, এ-কলেজের আবার ওই এক রয়েছে; ওয়েস্ট ব্লক বলতে হলঘরের হাট। একটা বড় হলঘরের তিনটে পার্টিশান আছে কাঠের—সেখানেই ওয়েস্ট ব্লকের ক্লাস বসে ভাগে ভাগে। পাশাপাশি ঘরে ক্লাস পড়লে ফুলরেণু আর পড়াতে পারে না, কাঠের পার্টিশান টপকে ওই লোকটার থিয়েটারি গলা ভেসে আসে, সংস্কৃত কাব্য পড়াচ্ছে, তার যত ব্যাখ্যা। রীতিমত অসভ্য। কিংবা বাংলা পড়াচ্ছে—সুর করে করে—কথায় কথায় হাসি উঠছে পাশের ঘরে। জ্বালাতন একেবারে। ফুলরেণু ক্লাসের মধ্যে রাগ করেছে, ক্লাসের বাইরে বেরিয়ে এসে ওই লোকটার ক্লাসের দরজার সামনে দাঁড়িয়েছে, লোকটা বেরিয়ে এলে বলেছে, “এভাবে গোলমাল হলে আমার পক্ষে ক্লাস করা যায় না।” লোকটা মুচকি হেসে বিনীত গলায় জবাব দিয়েছে, “ক্ষমা করুন। আমার ক্লাস শান্ত রাখছি, আপনি পড়ান।”
…ক্লাসের বাইরেও প্রফেসারদের ঘরে কথাটা তুলেছে ফুলরেণু, “আপনার ক্লাসে বড় গোলমাল হয়, আমি পড়াতে পারি না। কেমিষ্ট্রি একটা ছেলেখেলার সাবজেক্ট নয়।” স্বর্ণকমল হাত দুটি জোড় করে ঘাড় হেলিয়ে হেসে হেসে জবাব দিয়েছে, “আমি বড়ই লজ্জিত। রসশাস্ত্র আর রসায়নশাস্ত্রের তফাতটা ছেলেমেয়েরা বোঝে না। আমি ওদের বুঝিয়ে দি, মনে রাখতে পারে না।” ফুলরেণু গম্ভীর হয়ে জবাব দিয়েছিল, “আপনি নিজে মনে রাখলেই আমি খুশি হব।” লোকটা চটপট হেসে জবাব দিয়েছে, “আমি তো দিবারাত্রি স্মরণে রাখি।”…হাসিটা ফুলরেণুর ভাল লাগেনি। কী রকম যেন। আর ঘাঁটাতেও ইচ্ছে হয়নি।
বাংলা-সংস্কৃতের ওই স্বর্ণকমলের সঙ্গে তার চটাচটির ব্যাপারটা প্রফেসাররা জেনেছেন, ছেলেমেয়েরাও দেখেছে, জেনেছে। ফুলরেণুর তাতে খানিকটা রাগ বেড়েছে বই কমেনি। কিন্তু উপায় কি! স্বর্ণকমল দেড় বছর এখানে আছে, সিনিয়ার; সে মাত্র ছ’ মাস—জুনিয়ার। স্বর্ণকমলের নাকি খুঁটির জোর বেশি, তার বাবা মুঙ্গেরের নামকরা ডাক্তার ছিলেন, ধনী লোক, ভাইরা সব এক একটি দিক্পাল। ইনি ছোট, কাজেই বয়ে গেছেন আদরে, কাব্যটাব্য নিয়ে পড়ে আছেন।
তা যাক, ফুলরেণু এবার উঠল চেয়ার থেকে, মৃদুলার চিঠিতে যত ভাষার ছটা, পাকামি, অসভ্যতা, তাতে বেশ বোঝা যায় যে স্বর্ণকমলের প্রভাব ওতে আছে। ফুলরেণুর সন্দেহ নেই। কাল কলেজে গিয়ে মেয়ে প্রফেসারদের কাছে কথাটা তুলবে ফুলরেণু। বলবে, দেখুন আপনারা—ভেবে দেখুন, মেয়েদের স্বভাব-চরিত্র নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে আপনাদের যদি কোনও কিছু কর্তব্য না থাকে করবেন না কিছু। কিন্তু আমি সহ্য করব না। আমার সাধ্যমত আমি করব! ফাইট করব। না হলে কলেজ ছেড়ে চলে যাব।
ফুলরেণু আর-একটি সিদ্ধান্ত করে নিল। স্বর্ণকমল সপ্তাহে দুদিন এই হোস্টেলে ঊষা আর মমতাকে পড়াতে আসে, শখের টিউশানি; মেয়েদের হোস্টেলে ওর আসা বন্ধ করতে হবে। লোকটা ভয়ঙ্কর, ওর ছোঁয়াচে হোস্টেলের মেয়েদের মতিগতি খারাপ হতে পারে, ফুলরেণু তা হতে দিতে পারে না। তার একটা দায়িত্ব আছে।
চিঠিটা সন্তর্পণে ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দিল ফুলরেণু। সে ভেবে পেল না—কেমিষ্ট্রি মেয়ে মৃদুলার কি করে এইসব বাজে প্রেম-ফ্রেমে মাথা গেল! জগৎ-সংসারে জানা এলিমেন্ট এখন একশো আট, তার বাইরে যে কিছু নেই মৃদুলার তা জানা উচিত। তুমি সালফার ডায়োক্সাইডের প্রপারটিস লিখেছ, ডিসইনফেকটান্ট মানে যে জিনিস ছোঁয়াচের আক্রমণ থেকে বাঁচায়, তুমি…তুমি…ছি ছি—এইসব বাজে ছোঁয়াচে নোংরামির পাল্লায় পড়লে!
ফুলরেণুর নিজের মাথাই যেন লজ্জায় কাটা যাচ্ছিল।
মাথা ধরে যাচ্ছিল বলে ফুলরেণু পায়চারি করার জন্য ঘরের বাইরে এল। বাইরে এসে বারান্দা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ লক্ষ্য করল, মাঠ দিয়ে স্বর্ণকমল আসছে। আজ তার পড়াবার দিন নাকি? এত দেরি করে আসা কেন? কটা বেজেছে?
স্বর্ণকমলকে তাড়িয়ে দেবার ইচ্ছে হল ফুলরেণুর। কিন্তু উপায় নেই।
মাঝে মাঝে স্বর্ণকমল পড়াতে এসে তার সঙ্গে দেখা করে যায়। ভদ্রতার জন্য ফুলরেণু কিছু বলতে পারে না। কিন্তু ঘরেও ঢুকতে দেয় না। আজ ফুলরেণু ঠিক করল, স্বর্ণকমলের সঙ্গে দেখাও করবে না। ওর হোস্টেলে আসাও বন্ধ করতে হবে।
লোকটা বড় ছোঁয়াচে। ইভিল।
দুই
পরের দিন কলেজে এসে কথাটা তুলব তুলব করেও ফুলরেণু তুলতে পারল না। এ যা সৃষ্টিছাড়া কলেজ, যেমন সব মাস্টার-মাস্টারনি তাতে হুট করে একটা কথা তুলে সকলের কাছে হাস্যাস্পদ হওয়া বিচিত্র নয়। হয়ত তাকে নিয়ে আড়ালে হাসিঠাট্টা করবে, কাজের কথাটা কানেই তুলবে না। মৃদুলার চিঠিটা এক্ষুনি ওদের কাছে মেলে ধরতে চায় না ফুলরেণু। সেটা উচিত হবে না। তাতে ব্যাপারটা একেবারে হাটেবাজারে হয়ে যাবে। হাজার হলেও মৃদুলা মেয়ে এবং ছাত্রী; তার ভালবাসাবাসির চিঠি পুরুষদের চোখে পড়ুক এটা ফুলরেণু চায় না। সে যা করবে, শালীনতা ও সন্ত্রম বজায় দেখে করবে, গোপনে এবং যথাসাধ্য সতর্কতায়। ব্যাপারটা হই-হই করে করার নয়, হাটে হাঁড়ি ভেঙে জল ছিটানোর বিষয়ও নয়। চিঠিটা এখন থাক। ফুলরেণুর কাছে যেন ওটা বঁড়শি। প্রথমেই জোরজবরদস্তি করে টান মারতে গেলে ছিঁড়ে যেতে পারে, মাছের টাগরা থেকে খুলে যেতেও পারে; তখন আর করার কিছু থাকবে না। তার চেয়ে ধীরেসুস্থে বেশ করে খেলিয়ে তবে যা করার করতে হবে। ফুলরেণু শুধু যে মৃদুলাকে শিক্ষা দিতে চায় তা নয়, এই বেলেল্লা বেহায়া কলেজের চরিত্র শুধরে দিতে চায়, ভদ্র শালীন সভ্য করতে চায়। …তা ছাড়া আরও একটু নজর করার আছে, মৃদুলাকে নজর করতে হবে, অন্য ছেলেমেয়েদের, স্বর্ণকমলকেও। মেয়ে প্রফেসারদের কাছেই কথাটা আভাসে তুলবে ফুলরেণু প্রথমে, তুলে মনোভাবটা বুঝবে; তারপর তার ইচ্ছে পুরুষ প্রফেসারদের কিছু না জানিয়ে যদি কিছু করা যায় করবে, এমন কি, প্রিন্সিপ্যালকে যদি জানাতে হয় মেয়ে প্রফেসারদের তরফ থেকেই আড়ালে জানাতে হবে।
সেদিন আবার উমাদি আসেননি। উমাদির ওপরেই ফুলরেণুর একটু ভরসা আছে। উমাদি পুরনো লোক, বয়েস হয়েছে অনেকটা, এ-অঞ্চলের পুরনো নাম করা গোঁড়া ব্রাহ্ম পরিবারের মেয়ে, সভ্যতা শালীনতা মান্য করেন। কথাটা তাঁর কাছে তোলাই ভাল।
ফুলরেণুর সেদিন আর কিছু বলা হল না, কিন্তু ওয়েস্ট ব্লকের হলে ক্লাস নিতে গিয়ে পাশের ঘরে স্বর্ণকমলের পড়ানো কিছু কিছু শুনে রাখল। কাঠের পার্টিশানের ওপর থেকে যে কথাগুলো ভেসে আসছিল ফুলরেণু তার কিছুই বুঝছিল না; স্বর্ণকমল সংস্কৃত পড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে শুধু ফুলরেণু শুনছিল; ‘ফুলরেণু মদন’ ‘প্রিয়তমা রতি’ ‘বসন্ত’ ‘মকরন্দ’ ‘পর্যাপ্তপুষ্পস্তবকস্তানাভ্যঃ এইসব। শেষের কথাটা ফুলরেণু পুরোপুরি শুনতে এবং স্পষ্ট বুঝতে পরছিল না; তবু তার কান মুখ গরম হয়ে উঠছিল। এইসব অসভ্য শব্দ বইয়ে থাকে? নাকি স্বর্ণকমলের বানানো; সে বুঝে উঠতে পারছিল না। সংস্কৃত-টংস্কৃত পড়ানো উচিত না। ছি ছি!
পরের দিন কথাটা আভাসে তুলল ফুলরেণু। মেয়ে প্রফেসারদের ঘরে ওরা তখন তিনজন—উমাদি, ফুলরেণু আর বিজয়া। দুপুরের চা খেতে খেতে কথাটা ওঠাল।
“এদের আর সামলানো যায় না—” ফুলরেণু বলল।
উমাদি চেয়ারে পিঠ টেলিয়ে আলস্যের ভঙ্গিতে বসে খাচ্ছিলেন। বললেন, “তোমার ক্লাসে গোলমাল আর কোথায় হয়! দেখি না তো!”
ফুলরেণু চশমাটা খুলে মুছতে মুছতে বলল, “গোলমাল নয়। গোলমাল হওয়া তবু ভাল, তার চেয়েও বেশি হচ্ছে।”
বিজয়া কোলের ওপর মাথার কাঁটা খুলে রেখে খোঁপাটা সামান্য ঠিক করে নিচ্ছিল। এলাহাবাদের মেয়ে, বাঙালিদের মতন এলোমেলো করে খোঁপা রাখতে পারে না। দিনের মধ্যে পাঁচবার করে খোঁপা শক্ত করে। বিজয়া বলল, আমার সিভিকস ক্লাসে মার্কেট বসে যায়। কী গপ্ করে…বাসরে বাস।’
ফুলবেণু বিজয়ার মুখে প্রশ্রয় এবং হাসি ভিন্ন কিছু দেখল না। বিজয়া একেবারে বাজে। কিছু পড়াতে পারে না, নিজেই গল্পের রাজা ফাঁকিবাজ। তার ক্লাসে হুল্লোড় ছাড়া কিবা হবে আর। কিন্তু কথাটা তো ক্লাসের গোলমাল নিয়ে নয়। ফুলরেণু একচুমুক চা খেয়ে বলল, “আমাদের ডিসিপ্লিন থাকা দরকার।”
উমাদি যেন তেমন গা করলেন না কথাটায়, হাই তুললেন।
ফুলরেণু আবার বলল, “মেয়েদের ওপর অন্তত একটু নজর রাখা দরকার। এখানে যা হয় তাতে ভাল কিছু হচ্ছে না।”
উমাদি বললেন, “খারাপটা তো আমি কিছু দেখিনি। কেন, কি হয়েছে?”
ফুলরেণু চট করে কোনও জবাব দিল না। বিজয়ার সামনে যেন তার কথাটা বলতে ইচ্ছে নেই। আড়চোখে বিজয়াকে দেখল, তারপর সতর্ক হয়ে বলল, “আপনারা চোখ চেয়ে দেখেন না কিছু। দেখলেই বুঝতে পারতেন।”
উমাদির বোধ হয় ঘুম পাচ্ছিল, গরম পড়ে আসায় দিনের বেলায় আলস্য লাগছে; বড় করে হাই তুলে বললেন, “কই, আমার কিছু চোখে পড়ে না।”
“মেয়েদের খানিকটা সভ্যভব্য হওয়া উচিত”, ফুলরেণু বলল।
“তা অবশ্য উচিত—” উমাদি চায়ের বাকিটুকু চুমুক দিয়ে শেষ করলেন, রুমালে মুখ মুছলেন, তারপর বললেন, “মেয়েরা একটু চঞ্চল, হুড়মুড় করে। তা করুক। এই তো বয়েস। যত জীবন্ত হবে ততই ভরন্ত লাগবে। হইচই না থাকলে ওদের মানায় না।” বলে উমাদি হাই তুলতে তুলতে পানের ডিবে বের করে উঠে দাঁড়ালেন, পাশের ঘরে গিয়ে পান বিলোবেন পুরুষ মাস্টারদের, গল্পটল্প করবেন।
বিজয়া মাথার খোঁপা আট করে কাঁটা গুঁজে নিয়ে বলল, “মাসে দু’ডজন করে কাঁটা কিনি, মাগর খালি হারায়…।”
ফুলরেণু কোনও জবাব দিল না। বরং তার বিরক্তি হচ্ছিল, বিজয়া কলেজে পড়াতে আসে না মাথার চুল সামলাতে আর কাঁটা গুঁজতে আসে বলা মুশকিল। চুলের যত্ন শেষ হল, এইবার গিয়ে ছোকরা প্রফেসারদের সঙ্গে আড্ডা মারতে বসবে। যেমন কলেজ, তেমনি সব মাস্টারনি। ফুলরেণু নাকমুখ কুঁচকে ঘৃণার গন্ধে টেবিল থেকে একটা কাগজ টেনে নিয়ে মুখ আড়াল করল।
অথচ ব্যাপারটা এমন যেন ফুলরেণু ছেড়ে দিতে পারল না। স্বার্থ তার নয় কিছু মন্দ উদ্দেশ্যও তার নেই। সে তো ভালই করতে চাইছে, মন্দ নয়; মেয়েদের ভাল, কলেজের ভাল, সমাজের ভাল। মেয়েদের মা-বাবারও এতে উপকার বই অপকার হবে না, বরং তাঁরা যা জানেন না—তাঁদের লুকিয়ে লুকিয়ে যা চলছে সেই নোংরামিটা বন্ধ হবে।
কয়েকটা দিন ফুলরেণু তার মেয়ে সহকর্মীদের কাছে খুঁত খুঁত করল। স্পষ্ট কিছু বলল না, সরাসরি কারও নামও করল না, কিন্তু তার আপত্তি এবং অপছন্দটা প্রকাশ করতে লাগল।
“দেখুন, আমি ছেলেমানুষ নই”, ফুলরেণু একদিন ঘরভর্তি মেয়েদের কাছে বলল, “একটা প্রমাণ না থাকলে একথা আমি বলতাম না। যা হচ্ছে এখানে সেটা খুব খারাপ, মেয়েদের স্বভাব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।”
মিসেস চৌধুরী—মানে মনোরমা চৌধুরী বললেন, “তুমি যে কী বলতে চাইছ ফুলরেণু আমরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না।”
সুমিত্রা দেবী হেসে বললেন, “আরে বহিন, তুমি খালি বিল্লি বিল্লি ডাকছ! মাগর বিল্লি কাঁহা? পাত্তা দাও।”
ফুলরেণু রেগে বলল, “বেড়াল ঘরে না ঢুকলে আমি বলতাম না।”
“কোথায় বেড়াল?” উমাদি বললেন, “তুমি সেটা বলো, দেখাও।”
এরা অন্ধ। বেড়াল যে ঘরে ঢুকে দুধ মাছ শুঁকে যাচ্ছে, ঢাকা সরিয়ে মুখ দিয়ে পালাচ্ছে তা বুঝতে পারছে না। ফুলরেণু বলল, “বেড়াল আছে। আপনারা দেখতে চাইছেন না, তাই দেখতে পারছেন না!… এইটুকু এইটুকু মেয়ে তারা কি না করছে। কেমন করে শাড়ি পরে দেখেছেন?”
“তা ভাই, যখনকার যা চলন—” গীতাদি বললেন, “কলকাতা বম্বের হাওয়া এসেছে, পরবেই তো। ওদের সাজপোশাকে হাত দেওয়ার কিছু নেই আমাদের।”
“ঘাড়ে বুকে কাপড় রাখে না”, ফুলরেণু বলল, ঝাঁঝাঁলো গলায়।
“মুঙ্গের জেলায় গরমটা বেশি যে”—মনোরমা হাসতে হাসতে বললেন।
ফুলরেণুর মাথা আগুন হয়ে উঠল; বলল, “সেদিন একটা মেয়ে জল মুখে করে ন্যাকামি করছিল, একটা ছেলে তার গায়ে সুড়সুড়ি দিতে সে ছেলেটার জামায় কুলকুচো করে দিল।”
“এরকম দুষ্টুমি ওরা করে, ফুলরেণু। তুমি নতুন বলে তোমার চোখে লাগছে—আমাদের লাগে না।” উমাদি বললেন।
“এটা হেলদি সাইন” বিজয়া বলল, “রিলেশান ইজি থাকছে। কো-এডুকেশানে অ্যায়সেই হওয়া দরকার।”
ফুলরেণু প্রায় বিজয়াকে ধমকে উঠল, “কো-এডুকেশানে এরকম হয়। আপনি আমাকে শিক্ষা দেবেন না।”
উমাদি তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা সামলে নেবার চেষ্টা করলেন। “আমি একটা কথা বলি ফুলরেণু, হয়ত এখানকার ছেলেমেয়েরা একটু বেশি হই হই করে। কিন্তু ওটা ওদের দোষ নয়। এখানে এই রকমই হয়ে আসছে। তুমি স্বভাব চরিত্র খারাপ হবার কথা বলছ। আমরা এই কলেজে পুরনো কোনও স্ক্যান্ডেল কখনও হতে দেখিনি, শুনিনি। বরং এ রকম দেখেছি—এই কলেজেই পড়েছে এমন ছেলেমেয়েতে বিয়ে-থা হয়েছে পরে, যখন ছেলেরা আরও বড় হয়েছে, চাকরি-বাকরি ব্যবসাপত্র করেছে। ঠিক কিনা সুমিত্রা? তুমিই বলো।”
সুমিত্রা দেবী বললেন, “অনেক হয়েছে”, বলে গীতার দিকে তাকিয়ে হাসলেন।
গীতাদি বলল, “উমাদি, পাস্ট ইজ পাস্ট।”
সুমিত্রা জবাব দিলেন, “প্রেজেন্টয়েতেও হয় রে।”
সবাই হেসে উঠল, ফুলরেণু বাদে। ফুলরেণুর রীতিমত আত্মসম্মানে লাগছিল। সবাই মিলে তাকে উপহাস করল। কেউ বিশ্বাস করল না, মেয়েদের কতটা অধঃপতন হচ্ছে চরিত্রের। ফুলরেণু নিজের ব্যাগ থেকে টুকরো কাগজ বের করল, চোখ-মুখ তার লাল হয়ে উঠেছে রাগে, গলার স্বর চিকন ও তীক্ষ্ণ। কাগজটা বের করে ফুলরেণু বলল, “আমার ক্লাসে হাট বসেছিল। কি পড়ানো হচ্ছিল আপনারা শুনুন, আমি দু চারটে টুকে এনেছি !” বলে, ফুলরেণু পড়ল,…“তোমার মতো নবযুবতীরা যদি ইন্দ্রিয়সুখ জলাঞ্জলি দিয়ে তপস্যায় অনুরক্ত হয়, তা হলে মকরকেতুর মোহনশর কি কাজে লাগল ? সুন্দরী, তোমার নবীন বয়স, তোমার কোমল শরীর, শিরীষকুসুমের মতো সুকুমার অবয়ব। তোমার তপস্যার সময় এ নয়।…” ফুলরেণু থামল, তার চোখমুখ লালচে, কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা। “এইরকম আরও আছে। আমার মনে থাকে না। কিন্তু বুঝতে পারি যা পড়ানো হচ্ছে তা আগলি।…সেদিন শুনছিলাম বলা হচ্ছে : ‘সরোবরের জল দিন দিন যেমন বাড়ে, তেমনি নারী নিতম্…’ বলতে বলতে থেমে গেল ফুলরেণু। অনেক কষ্টে জিব আটকাল।
মেয়েরা চুপ। গীতাদি হঠাৎ হেসে বললেন, “আপনি ভাই বড় বেরসিক। স্বর্ণকমলবাবু আলাদা কী আর পড়াতে পারেন। বোধহয় কাদম্বরী পড়াচ্ছিলেন। ওদের খানিকটা ‘কুমার সম্ভব’—আর বোধহয় ‘শকুন্তলা’র দু-একটা অংশ আছে।” গীতাদি নিজে বাংলা পড়ান।
ফুলরেণু বলল, “কাদম্বরী-টরী জানি না, আপনারা জানবেন। ওসব নোংরা জিনিস পড়ে কি হয় ?”
“বলছেন কি ভাই আপনি ! ‘কাদম্বরী’, ‘রঘুবংশ’, ‘মেঘদূত’, ‘শকুন্তলা’—এ সব হল আমাদের প্রাচীন কাব্য, কত নামকরা বই, সংস্কৃত সাহিত্যের মণিমাণিক্য, এসব না পড়লে সংস্কৃত পড়া হবে কেন !”
“পড়তে হবে না।”
“হবে না ?”
“আমি হলে সংস্কৃত পড়া বন্ধ করে দিতাম। কথায় কথায় শুধু নলিনী আর মালিনী…।”
“পীনপয়োধরও আছে—” গীতাদি উলটো ঠাট্টা করলেন, “আলপিন নয় কিন্তু…।”
উমাদি তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা থামিয়ে দিয়ে বললেন, “যাকগে—যাকগে, যেতে দাও। সব পড়াই পড়া। পড়ার মধ্যে দোষ কিছু নেই।…আমি বলি কি ফুলরেণু, তুমি মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখো। কলেজের ছেলেমেয়েরা তো শিশু নয়, তারা নিশ্চয় খানিকটা বোঝে। যা বোঝে না, তা না বুঝুক। বয়েস হয়েছে—জগতের কিছুটা বুঝবে বই কি ! তোমার যদি কোনও আপত্তি থাকে, কারও সম্পর্কে কোনও কমপ্লেন থাকে, তুমি প্রিন্সিপ্যালকে বলতে পারো, আমাদেরও পারো।”
ফুলরেণুর মাথার ঠিক ছিল না, রাগে অপমানে জ্বলছিল। বলল, “আপনারা যা করেছেন তাতে ছেলেমেয়েদের মাথা খাওয়া হচ্ছে। নয়তো ওইটুকু মেয়ে ভালবাসাবাসির চিঠি লেখে ?”
উমাদি, সুমিত্রা, মনোরমা, গীতা, বিজয়া—সবাই ফুলরেণুর দিকে তাকিয়ে থাকল। নয়ন বুঝি অপলক হল একটুক্ষণ।
মনোরমা বললেন, “ওমা, তাই নাকি ! কোন মেয়ে ?”
ফুলরেণু নাম বলল না। “নাম জেনে কি হবে ! এই কলেজেরই ছাত্রী, আপনাদেরই স্টুডেন্ট…”
বিজয়া পরম কৌতুকে জিজ্ঞাসা করল, “কোন ইয়ার ? আর্টস না সাইন্স ?”
বিজয়ার কথায় ফুলরেণুর ঘেন্না হচ্ছিল ! এটা কি তামাশার কথা ? কিছুই বল না ফুলরেণু।
উমাদি সিঁথির কাছে কাঁচাপাকা চুলের কাছটা একটু চুলকোলেন। সুমিত্রার মুখের দিকে তাকালেন সামান্য, তারপর বললেন, “আমি আর কী বলব ! যে বয়েসের যা⋯! এরা তবু উনিশ-কুড়িতে লিখছে, আমি ষোলো সতেরোয় লিখেছি…।”
উমাদির কথায়, সকলে কলরোল তুলে হেসে উঠল। ফুলরেণুর মনে হল সবাই মিলে তাকে নিয়ে তামাশা করল, উপহাস করল, একশেষ করল অপমানের। তার একমাত্র ভরসা ছিলেন উমাদি, সেই উমাদিই তাকে সকলের সামনে এমন ভাবে অপ্রস্তুত করলেন যে লজ্জায় অপমানে তার মাথা কাটা গেল।
আর কিছু বলল না ফুলরেণু ; কলেজ ছুটি হয়েছে, ঘর ছেড়ে চলে গেল।
ফুলরেণু বুঝতে পেরেছিল উমাদিদের দিয়ে কিছু হবে না। এরা এই কলেজের ধাত পেয়েছে, সব ব্যাপারেই হেলাখেলা, তামাশা ; দায়দায়িত্ব কর্তব্য নিয়ে মাথা ঘামানোর কথা এরা ভাবে না। সভ্যতা শালীনতার জন্য মাথাব্যথা এদের হবার কথা নয়, যদি সে জ্ঞান থাকত তবে পুরুষ প্রফেসারদের ঘরে বসে অত গল্প গুজব, হাসি, পান-জরদার আসর জমাত না। নিতান্ত এদের বয়েস হয়েছে, ছেলেপুলে আছে—ঘরসংসার করে নয়ত বয়েস কমিয়ে এই গোয়ালে ঢুকিয়ে দিলে ওই ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে এরাও সমান মিশে যেত !
যাক, এরা চুলোয় যাক। ফুলরেণু ওদের মতন হতে পারে না, পারবে না। যা করার সে একলাই করবে। সহকর্মীদেরই যখন পাওয়া গেল না, তখন পুরুষদেরও সাহায্য পাওয়া যাবে না। পুরুষদের সাহায্য নেওয়ার কথা অবশ্য ফুলরেণু আগে ভাবেনি। তবে এটা পাওয়া গেলে, ওটা পাওয়া যেতে পারত হয়ত। না পেয়েছে না পাক, কথাটা সে সরাসরি প্রিন্সিপ্যালের কাছে ওঠাবে। তার আগে তাকে একটু খোঁজ খবর নিতে হবে। মামলা সাজিয়ে না নিয়ে মোকদ্দমা লড়তে যাওয়ার মতন বোকামি সে কবে না।
তিন
সেদিন হোস্টেলে মমতাদের ঘরে এসে ফুলরেণু বলল, “মমতা, তোমার সংস্কৃত বইখানা দেখি।”
মমতা কেমন ঘাবড়ে গিয়েছিল, কিছুই বুঝতে পারছিল না। বলল, “কোন বই, দিদি ?”
“ক্লাসে যা পড়ানো হয়…”
“আমাদের চারটে বই। একটা বই সিলেকসানের মতন, অন্য তিনটে…”
“একটাই আগে দাও।”
মমতা একটা বই এনে হাতে দিল।
ফুলরেণু বইটা হাতে নিয়ে পাতা খুলল। “এ আমি কি বুঝব ! সংস্কৃত টংস্কৃত আমি জানি না। মানের বই নেই ?”
মমতা এবার যেন বুঝল একটু। বলল, “বাংলা আছে, দিচ্ছি।”
বইয়ের ডাঁই থেকে মোটা মতন একটা বই এনে ফুলরেণুর হাতে দিল মমতা। বলল, “এটায় দিদি, বাংলা হরফে সংস্কৃত লেখা আছে, মানে দেওয়া আছে বাংলায়। খুব সুন্দর…”।
ফুলরেণু পাতা উলটে এক লহমা দেখে নিল। কালিদাস গ্রন্থাবলি…। বলল, “তোমাদের এ বই সবটা পড়ানো হয় ?”
মমতা মাথা নাড়ল। “না, ওটা পড়ানো হয় না ; ওর থেকে দুটো কাব্যের চারটে সর্গ পড়ানো হয় !”
“কোনটা কোনটা ?”
“রঘুবংশম্ আর অভিজ্ঞান শকুন্তলম্…” মমতা বলল, কোন কোন সর্গ তাও বলল।
ফুলরেণু বই নিয়ে ফিরে আসতে আসতে বলল, “তোমাদের উনি পড়াতে এলে বলবে যাবার সময় যেন আমার সঙ্গে কথা বলে যান।” স্বর্ণকমলের নামটা ইচ্ছে করেই ফুলরেণু বলল না।
মমতা মাথা হেলিয়ে বলল, “আজ তো উনি আসবেন না, কাল আসবেন। এলে বলব।”
ফুলরেণু চলে গেল।
এতক্ষণ রেবা ঘরের একপাশে বসে কত যেন মন দিয়ে সেলাই করছিল। ফুলরেণু চলে যেতেই মাথা উঠিয়ে চোখ ভরা হাসি নিয়ে বলল, “কী ব্যাপার রে ?”
“কী জানি !”
“কার্বন ডায়োক্সাইড কালিদাস পড়বে ! বাব্বা, এর চেয়ে নাইনথ ওয়ান্ডার আর কিছু নেই। কাল সকালে উঠে দেখবি সূর্য পশ্চিম দিকে উঠেছে।”
“ইচ্ছে হয়েছে পড়বার… !”
“ইচ্ছে !…তুই একেবারে নেকু মমতা। ইচ্ছে-টিচ্ছে নয়, চাপ—প্রেশার। জামাইবাবু চাপ দিয়েছেন, ভাল ভাল ভাষা দিয়ে কথাটথা বলতে হবে তো। পরশু বকুলের কাছ থেকে দিদি ‘চন্দ্রশেখর’ ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’-টুইল নিয়ে গেছেন…বকুল বলছিল।”
মমতা হেসে ফেলল। “তুই এত জানিস, বাবা !”
রেবা ঘাড় দুলিয়ে কটাক্ষ করে বলল, “জানব না কেন ! সবাই জানে। গলা টিপলে দুধ বেরোবার বয়স আমাদের নেই। জামাইবাবু এলে দিদির যেমন হয় দেখিস না। বারান্দায় এত পায়চারি কিসের ? অত গঙ্গা গঙ্গা বলে গঙ্গাদিকে ডাকাই বা কেন ?”
মমতা হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বলল, “ওই বইটা আমার নয় রে ! আমাদের জামাইবাবুর। আমি ভাল বুঝতে পারি না বলে দিয়েছিলেন পড়তে।”
রেবা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ে বলল, “তুই পাতায় পাতায় যাস।”
রাত্তিরে ফুলরেণু নিজের ঘরে বসে কালিদাস গ্রন্থাবলি পড়ছিল। পড়তে পড়তে সে প্রায় পাথর হয়ে গিয়েছে। চোখের সামনে যে পাতাটা খোলা তার দিকে অনেকক্ষণ আর সে তাকাতে পারল না। সর্বাঙ্গ যেন ফাল্গুনের গরমে জ্বালা করছে, চোখ মুখ লাল, ঠোঁটের ডগায় দাঁতের চাপ বসে লাগছিল। নিশ্বাস গরম। অনেকক্ষণ পরে কোনও রকমে নিজেকে সামান্য সামলে নিয়ে ফুলরেণু পাতাটার দিকে আবার তাকাল। নীচের দিকে বাংলা তর্জমা। ফুলরেণু আচ্ছন্নদৃষ্টিতে পড়ল :…“সেই মুহূর্তে বায়ুবেগে পার্বতীর পরিধেয় বস্ত্র অপসারিত হইলে তাঁহার ঊরুমূলে নখচিহ্ন সমূহ দেখিয়া তৎপ্রতি শিবের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। পার্বতী শিথিল বসন বন্ধন করিতে উদ্যত হইলে মহাদেব প্রিয়তমাকে নিবারণ করিলেন। রাত্রি জাগরণ হেতু পার্বতীর নয়ন রক্তবর্ণ, গাঢ় দন্তক্ষত হেতু অধর প্রপীড়িত এবং অলকাবলী ছিন্নভিন্ন হইয়াছিল…।”
ফুলরেণু আর পড়তে পারল না। কপাল, গাল, গলা, ভীষণ জ্বালা করছিল ; নিজের নিশ্বাসের গরমটা অনুভব করে তার মনে হল তার জ্বর এসেছে। হাতের তালুতে ঘাম জমে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি বই বন্ধ করে ফেলল। চোখের পাতা বুজে যেন সে আর কিছু দেখছে না, তাকে কেউ দেখছে না—এই ভাব করে বসে থাকল ! কী বিচ্ছিরি, কী যাচ্ছেতাই। ছি ছি। মেয়েরা এই সব পড়ে ? শিব তো গাঁজা খায় জানত ফুলরেণু, একেবারে ক্ষ্যাপা, বোমভোলা লোক। অথচ এ সব কী ? সে নিজে মদ খাচ্ছে, পার্বতীকে খাওয়াচ্ছে…আর যা যা করছে—ছি ছি…।
ফুলরেণু উঠে পড়ল, উঠে পড়ে জল দেখল। তারপর মুর্ছা যাবার মতন করে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল।
পরের দিন সকালে কলেজে পড়াবার কেমিস্ট্রি বইটা খুলে বসল ফুলরেণু। চোখ মুখ গম্ভীর, থমথমে গলার স্বর ভারি যেন কাল সারারাত ঘুম হয়নি, গরমে জানলা খুলে রেখে ঠাণ্ডা লেগেছে, নাকের ডগায় জল আসছে বার বার। কেমিস্ট্রি বই খুলে অ্যাসিডের চ্যাপ্টারটা বের করল। পড়ার কিছু নেই ; তবু বার কয়েক অ্যাসিডের চ্যাপ্টার পড়ল। আজ ফার্স্ট ইয়ারে অ্যাসিড পড়াবে ফুলরেণু।
কালিদাস গ্রন্থাবলির দিকে কিছুতেই আর তাকাবে না ফুলরেণু। তাকাবে না বলেই বাসি খবরের কাগজটা চাপা দিয়ে বইটা আড়াল করে রেখেছে।
অ্যাসিড পড়া শেষ করে ফুলরেণু যখন উঠল তখন তাকে অ্যাসিডের মতনই তীব্র দেখাচ্ছিল। হয়ত সেটা শরীর খারাপের জন্য।
কলেজ থেকে তাড়াতাড়ি ফিরল ফুলরেণু। আজ শেষের দিকে ক্লাস ছিল না। অন্য সময় হলে সে থাকত, এতটা রোদে আসত না, গল্পগুজব করে সময়টুকু কাটিয়ে বিকেলের গোড়ায় ফিরত। আজ থাকল না। থাকতে ইচ্ছে করল না। মনোরমা চৌধুরী আর বিজয়া বসে গল্প করছিল। ওদের সঙ্গ অসহ্য লাগে আজকাল ! শরীরটাও ভাল নেই। আলস্য আর জ্বর জ্বর লাগছে, বেশ ব্যথা হয়েছে গায়ে কোমরে। টাঙা ডাকিয়ে এনে টাঙায় চড়ে ফুলরেণু ফিরে এল হোস্টেলে। হোস্টেল খাঁ খাঁ করছে। ঝি বামুন ছাড়া কেউ নেই। রোদের কী তাত এখনও। ধুলোভরা বাতাস উড়ছে। কাক ডাকছিল, একা একা।
ঘরে এসে ফুলরেণু শাড়ি বদলাল, চোখে মুখে জল দিয়ে এসে অ্যাসপিরিন ট্যবলেট খেলে গোটা দুই : দরজা ভেজিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল। খানিকটা ঘুমোতে পারলে ভাল হত। কিন্তু এতটা অবেলায় ম্যাজমেজে শরীর নিয়ে ঘুমোত সাহস হল না। ঘুমও পাচ্ছিল না। কোমরের কাছটায় এত ব্যথা হলে রাত্রে হট ওয়াটার ব্যাগ দিতে হবে।
এ-পাশ ও-পাশ করে, চোখ বুজে, কখনও চোখ খুলে শুয়ে, নোট লিখেও সময় যেন ফুরোচ্ছিল না। হাই উঠছিল। টুকরো কয়েকটা শব্দ ছাড়া কোনও কিছু কানেও আসছে না। কাশীর কথা মনে পড়ল। মার চিঠি আসেনি দিন সাতেক ; টোকনটাও চিঠিপত্র দিচ্ছে না। কী ব্যাপার কে জানে ! সামার ভেকেশানের এখনও দেরি। সবে তো দোল এল।
ফুলরেণু সময় কাটানোর জন্য আলস্যভরে ‘কৃষ্ণকান্তের উইল’ তুলে নিল ! তারপর পাতা উলটোতে লাগল। পড়তে শুরু করেছিল সেদিন, মাঝপথে ফেলে রেখেছে। পাতা খুঁজে নিয়ে আবার পড়তে লাগল : “তুমি, বসন্তের কোকিল। প্রাণ ভরিয়া ডাক তাহাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কিন্তু তোমার প্রতি আমার বিশেষ অনুরোধ যে, সময় বুঝিয়া ডাকিবে।…” এ সব বই ফুলরেণু দু-চারটে এক সময়ে পড়েছিল, তখন বোঝার মতন মন হয়নি, আগ্রহও হয়নি। কী হবে এ সব পড়ে, তার চেয়ে শক্ত একটা কেমিক্যাল কম্পোজিশান বোঝা ভাল। সেটা বুঝতে বুঝতে কলেজ জীবনটা কাটাল। তারপর এক জায়গায় চাকরি করছিল পড়ানোর, বছর খানেক সেখান থেকে এখানে—এই মুঙ্গের জেলার দীপনারায়ণ জুবিলি কলেজ।
‘রোহিণীর কলসী ভারি, চাল-চলনও ভারি। তবে রোহিণী বিধবা।’…ফুলরেণু পড়ে যাচ্ছিল। হাই উঠছে। জানলার বাইরে বাতাসের ঝাপটা লেগে জানলায় শব্দ হল, কাকটা ডাকছে এখনও।
‘…অমনি সে রসের কলসী তালে তালে নাচিতেছিল। হেলিয়া দুলিয়া, পালভরা জাহাজের মতো, ঠমকে ঠমকে, চমকে চমকে, রোহিণী সুন্দরী সরোবর পথ আলো করিয়া জল লইতে আসিরেছিল—এমন সময় বকুলের ডালে বসিয়া বসন্তের কোকিল ডাকিল। কুহুঃ কুহুঃ কুহুঃ…।’ ফুলরেণু অন্যমনস্ক হল, বইয়ের পাতায় মন থাকল না। বরং তার কেমন একটা কৌতূহল—বসন্তের কোকিলকে সময় বুঝে ডাকতে বলার অর্থটা কি ? হেঁয়ালি নাকি ? কখন ডাকবে ? কোন সময়ে ?
ফুলরেণু চোখের পাতা আধবোজা করে ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকল। ভাল লাগছে না। কেমন উদাস লাগছে। তা যতই বল, কালিদাসের চেয়ে এই কৃষ্ণকান্তের উইল সভ্য। মেয়েরা পড়তে পারে।
ফুলরেণুর যেন তন্দ্রা এসে গিয়েছিল।
কতক্ষণ পরে, ঠিক খেয়াল নেই, ফুলরেণু সাড়া পেল। মেয়েরা ফিরেছে? তাদের গলা পাওয়া যাছিল। বিকেল হয়ে গেছে।
রাতের দিকে স্বর্ণকমল এল।
বাইরে থেকে সাড়া দিয়ে ডাকল। ফুলরেণু অপেক্ষা করছিল। বলল, “ভেতরে আসুন।”
স্বর্ণকমল ঘরের মধ্যে এল।
ফুলরেণু আগে ভেবেছিল, লোকটাকে ঘরে ঢুকতে দেবে না, বারান্দায় দাঁড় করিয়ে রেখে কথা বলবে, বা নীচে মাঠে নিয়ে গিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কথা বলবে। পরে ভেবে দেখল, এটা দৃষ্টিকটু দেখাবে। মেয়েরা দেখবে, ঝি বামুনরা দেখবে। ফুলরেণু রাগের মাথায় একটু জোরেই কথা বলে, বাইরে জোরে জোরে কথা বললে মেয়েদের কানে যেতে পারে। তার চেয়ে ঘরেই কথাবার্তা বলা ভাল। তা ছাড়া শরীরটাও ভাল নেই, বাইরে যেতে ইচ্ছেও করছিল না।
“আপনি আমায় দেখা করতে বলেছিলেন, মমতা বলছিল”, স্বর্ণকমল বিনয় করে বলল।
“হ্যাঁ—বসুন।”
স্বর্ণকমল বসার জায়গা খুঁজল। ফুলরেণু চেয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে, হাত কয়েক তফাতে একটা টুল। চোরা চোখে বিছানাটাও একবার দেখে নিল স্বর্ণকমল। তারপর ইঙ্গিতে টুলটা দেখিয়ে বলল, “ওখানেই বসি ?”।
ফুলরেণু তাকিয়ে দেখল। মনে মনে বলল : হ্যাঁ—ওখানেই বসো—ওই টুলে ; টুলটা উঠিয়ে দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে বাইরে বসলেই ভাল হত। কিন্তু তা তো বলতে পারি না, হাজার হোক ‘কোলিগ’। নিতান্ত যেন খারাপ দেখাবে, অসৌজন্য প্রকাশ পাবে বলে ফুলরেণু স্বর্ণকমলকে টুলের ওপর বসতে বলতে পারল না। চেয়ারের পাশ থেকে সরে যেতে যেতে ফুলরেণু বলল, “না না, ওখানে কেন, এই চেয়ারে বসুন।” বলে বিছানার দিকে চলে গেল।
স্বর্ণকমল চেয়ার টেনে নিল। “আপনি বসবেন না?”
“বসছি ; আপনি বসুন।”
স্বর্ণকমল বসল।
ফুলরেণু হাতের ঘড়ি দেখল। আটটা বেজে মিনিট পাঁচেক হয়েছে। সন্ধের আগে আগেই ঘড়িটা হাতে পরে নিয়েছে ফুলরেণু, যেন হিসেব রাখছে স্বর্ণকমল কখন পড়াতে এল কতক্ষণ পড়াল, তার সঙ্গে কখন দেখা করতে এল।
কথাটা ঠিক কীভাবে শুরু করা যায় ফুলরেণু বুঝতে পারছিল না। মনে মনে যা ভেবে রেখেছে—সেসব নিশ্চয় বলবে পরে, কিন্তু প্রথমে কি বলা যায় ! ফুলরেণু অস্বস্তি বোধ করল। বিছানার ওপর বসবে কি বসবে না ভাব করে দাঁড়িয়ে জানলার দিকে তাকিয়ে থাকল। দিন তিনেক পরেই দোল পূর্ণিমা। বাইরে চাঁদের আলো টলটল করছে, জানলায় জ্যোৎস্না এসে পড়েছে।
কথা শুরু করার আগে স্বর্ণকমলকে একবার লক্ষ্য করল ফুলরেণু। চেহারাটা দেখলেই বোঝা যায়—লোকটা খুব চালাক-চতুর। ছলছলে হাসিখুশি মুখ হলে কি হবে, ওই সুন্দর কার্তিকঠাকুরের মতন মানুষটা ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড ধূর্ত।
অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল ফুলরেণু। তারপর যেন তৃতীয় কাউকে উদ্দেশ করে কিছু বলছে, বলল, “হোস্টেলের মেয়েদের ঘরে বসে পড়ানোর ব্যাপারে একটা অসুবিধে হচ্ছে। একটা ঘর দেড় দু ঘণ্টা আটকে থাকে…অন্য বোর্ডারের অসুবিধে হয়।”
স্বর্ণকমল শুনল। হাসি হাসি মুখ করে বলল, “মমতার ঘরে বসে পড়াব না বলছেন?”
“রেবার অসুবিধে হয়। সে অন্য ঘরে গিয়ে বসে থাকে, গল্প করে।”
“ঊষা যখন এ-ঘরে—মমতার ঘরে এসে আমার কাছে পড়ে, রেবা তখন উষার ঘরে যেতে পারে।”
“না, নিজের জায়গা ছেড়ে অন্য ঘরে গিয়ে পড়াশোনা হয় না।”
“ও !”
সামান্য অপেক্ষা করে ফুলরেণু বলল,“মেয়েরা আমায় কেউ কিছু বলেনি। কিন্তু আমার একটা দায়িত্ব আছে। সকলেরই সুবিধে অসুবিধে আমার দেখা দরকার।”
স্বর্ণকমল প্রতিবাদ করল না, বরং সমর্থন জানিয়ে মাথা নাড়ল। “তা যথার্থ। তা হলে অন্য কী করা যায় ?” স্বর্ণকমল যেন আদেশের অপেক্ষায় ফুলরেণুর দিকে তাকিয়ে থাকল।
ফুলরেণু কোন জবাব দিল না। দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল, পা যেন কাঁপছে, হাঁটুর ওপরটায় ব্যথা-ব্যথা। বাধ্য হয়েই ফুলরেণু বসল।
স্বর্ণকমল বলল, “নীচে একটা ঘর আছে না ? কোনার দিকে ?”
ফুলরেণু অবাক হয়ে তাকাল। “আছে এক ফালি ঘর। ঝিদের ঘরের পাশে। কেন ?”
“তা হলে ওখানে বসে ওদের পড়াই।”
ফুলরেণু এ দিকটা একেবারে ভেবে দেখেনি। চালে হেরে যাওয়ার মতন অবস্থা হল তার। বিপন্ন বোধ করে হঠাৎ বলল, “ওই ঘরটা, আমি সিকরুম করব ঠিক করেছি।” বলে অনেকটা নিশ্চিত হল যেন ফুলরেণু। উলটো চালটা যেন সামলে নিয়েছে। মনে মনে ভাবল, লোকটা কী চালাক ! এ তবুও অন্য পাঁচটা ঘরের মধ্যে ছিল, নীচে যাওয়া মানে আড়ালে পালানো। ওখানে বসে মেয়ে দুটোকে পড়াবে না ছাই, একেবারে পাকিয়ে ছাড়বে।
স্বর্ণকমল বলল, “সিকরুম করবেন ওটা?”
“হ্যাঁ।”
“তবে তো ভালই—”
“ভাল কিসের ?”
“সিক আর ক’টা বছরে ! খালিই পড়ে থাকবে। ওখানেই বেশ পড়ানো চলবে।”
ফুলরেণু অবাক চোখ করে স্বর্ণকমলকে দেখল। লোকটা কি মুখটিপে হাসছে নাকি ! মুখ বেশ চকচক করছে, কী ফরসা রং, স্নো পাউডার মেখে পড়াতে আসে নাকি ও ?
বাইরে গঙ্গার গলা। পরদা সরিয়ে দিতে বলছে। ফুলরেণু কিছু বুঝল না। স্বর্ণকমল উঠে দরজার কাছে গিয়ে পরদা সরাল। গঙ্গা ঘরে এল, হাতে দু কাপ চা। ফুলরেণু বুঝতে পারল না গঙ্গাকে কে চা আনতে বলেছে।
স্বর্ণকমল হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিল। গঙ্গা অন্য কাপটা ফুলরেণুর হাতে দিতে গেল। প্রায় ধমকে উঠে কিছু বলতে যাচ্ছিল ফুলরেণু, অনেক কষ্টে সংযত করল নিজেকে। “এখন চা ?”
স্বর্ণকমল হাসিমুখে বলল, “খান। চায়ে কিছু হয় না।…আমি আসবার সময় মমতাদের বলে এসেছিলাম। পাঠিয়ে দিয়েছে।”
ঝিয়ের সামনে কিছু বলা যায় না, উচিতও নয়, ফুলরেণু চায়ের কাপ নিল। ভেতরে ভেতরে রেগেছে। আমার হোস্টেলে এসে তুমি আমাদের মেয়েদের চায়ের ব্যবস্থা করে দিতে বল ? এ প্রায় ধৃষ্টতা !
গঙ্গা চলে গেল। স্বর্ণকমল চেয়ারে বসে চা খেতে খেতে তৃপ্তির শব্দ করল বার কয়েক। ফুলরেণু চায়ের পেয়ালায় মুখ ছোঁয়াল না।
স্বর্ণকমল বলল, “তা হলে ওই ব্যবস্থাটাই ভাল হল, নীচের ঘরে—মানে সিকরুমেই আমি মমতাদের পড়াব।”
ফুলরেণু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বোধ হয়, কথাটা কানে যেতেই হঠাৎ তার খেয়াল হল। শক্ত গলায় বলল, “না।”
“না— ! না কেন ?” স্বর্ণকমল যেন কতই অবাক হয়েছে এমন চোখে তাকাল।
“সিকরুম পড়বার জায়গা নয়।”
“কিন্তু ওটা যখন খালিই পড়ে থাকবে—”
“কে বলেছে খালি পড়ে থাকবে !”
“না, মানে—তেমন কিছু বড় রোগ—বসন্ত, হাম, কলেরা, টাইফয়েড না হলে তো আপনি কাউকে সিকরুমে পাঠাচ্ছেন না। এখানে রোগটোগ বড় হয় না। মেয়েদের হবে না বলেই মনে হয়।”
“আপনার কি মনে হয় না হয় আমার তা জানার দরকার নেই। যে কোনও রকম অসুখ করলেই আমি মেয়েদের সিকরুমে পাঠাব।”
“সর্দি-কাশি হলেও ?”
“হাঁ, হাঁচি হলেও।”
স্বর্ণকমল ঢোঁক গিলল। তার চোখ চকচক করছে। পরে বলল, “আমার বাড়ি অনেকটা দূরে। মাইল খানেক। মমতাদের গিয়ে পড়ে আসতে কষ্ট হবে।”
পাগল নাকি ফুলরেণু। তোমার বাড়িতে তুমি একলা থাক, সেখানে এই সব মেয়েকে পড়তে পাঠাবে ফুলরেণু। তা হলে এখানে যাও বা পদার্থ আছে তোমার কাছে গেলে তার কিছু থাকবে না। ওই সব অসভ্যতা পড়বে, তুমি পড়াবে, আর মেয়েগুলোর ইহকাল একেবারে নষ্ট হবে।
ফুলরেণু বলল, “দূরে গিয়ে পড়া বিশেষ করে রাত্রে আমি অ্যালাও করতে পারি না।’
স্বর্ণকমল চুপ।
ফুলরেণু এবার অন্যমনস্কভাবে কাপে কয়েক চুমুক দিল। দিয়ে ভালই লাগল। গলাটা ভারি হয়ে জড়িয়ে এসেছিল, আরাম লাগল। সংস্কৃত বাংলার প্রফেসার এবার জব্দ।
স্বর্ণকমল শেষে বলল, “আপনি যেরকম বলছেন তাতে তো আর পড়ানো হয় না।”
মনে মনে খুশি হল ফুলরেণু। কে তোমায় পড়াতে বলেছে। তোমার পড়ানো বন্ধ করতেই তো চাই।
স্বর্ণকমল বেশ মনোযোগ দিয়ে ফুলরেণুকে লক্ষ করল। তারপর দুশ্চিন্তার ভাব করে বলল, “প্রিন্সিপ্যালকে তা হলে একবার কথাটা বলি, কি বলেন ?”
“কেন প্রিন্সিপ্যালকে কেন—?”
“উনিই পড়াতে বলেছিলেন। ওঁকে না জানিয়ে কিছু তো করা যায় না।”
ফুলরেণু এবার সমস্যায় পড়ল। প্রিন্সিপ্যালকে এখনই কথাটা জানানো কি উচিত হবে ? তাঁর কানে কথাটা উঠলে ফুলরেণু কি ধরনের কৈফিয়ত দেবে এখনও তা ঠিক করে উঠতে পারেনি। স্বর্ণকমলের বিরুদ্ধে তার মামলা এখন পর্যন্ত সাজানো হয়নি।…বেশ মনমরা হয়ে গেল ফুলরেণু। বলল, “অন্য ব্যবস্থা কী করা যেতে পারে আমি এখনও ভাবিনি। ভেবে দেখি। তারপর যা হয় করব। আপনি পরে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।”
স্বর্ণকমল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। “কবে দেখা করব ?”
“করবেন। দু একদিন পরে করবেন। শুক্রবার নাগাদ।”
এক মুহূর্ত ভাবল স্বর্ণকমল। “শুক্রবারই দেখা করব।”
“করবেন।”
“সন্ধের দিকে !”
মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল ফুলরেণু। স্বর্ণকমল যাবার জন্য পা বাড়িয়ে বলল, “আপনার শরীর তেমন ভাল নেই, না ?”
“না !”
“শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে তাই…’ স্বর্ণকমল দু পা এগিয়ে প্রায় ফুলরেণুর মুখোমুখি হল, জানলার দিকে তাকাল, তারপর বলল, “বসন্তের এই বাতাসটা ভাল না। …কা ললনা দিবসন্তং কুসুমশরমসোয় হৃদ্যনাদিবসন্ত…” বলতে বলতে হাসিমুখে স্বর্ণকমল দরজার দিকে এগিয়ে গেল।
ফুলরেণু কিছু বুঝল না। কী বলল, স্বর্ণকমল ? কি মানে ওই বিদঘুটে কথাটার ?
বাইরে বেরিয়ে এসে স্বর্ণকমল হাসল। মনে মনে শ্লোকটার তর্জমা করল : বসন্তের এই দুরন্ত সময়ে, এমন কোন কামিনী আছে যে হৃদয়স্থিত ফুলবান মদনকে সহ্য করতে পারে ? কেউ পারে না সখি, কেউ পারে না।
চার
সারাটা দিন মেয়েরা রং খেলছে। সেই যে দল মিলে ভূত সেজে বেরিয়ে গিয়েছিল সব, সারা শহর বন্ধুবান্ধবদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে হল্লা করে রং মেখে ঘুরে বেড়িয়েছে। হোস্টেলে ফিরেছিল বেশ বেলায়। স্নান খাওয়া করে জিরিয়ে আবার সব বেশবাস করে বেরিয়ে গেল ; মেয়েদের হাতে গায়ে কানে তখনও রঙের আবছা দাগ, চুলের তলায় আবিরের আভা। ওরা গেছে দুর্গাবাড়িতে ‘পূর্ণিমা মিলনে’, সেখানে আজ গান বাজনা। যাবার সময় বলে গেছে অবশ্য ফুলরেণুকে। ফুলরেণু নিষেধ করেনি। করা উচিত হত না। সুমিত্রা দেবী, মনোরমা চৌধুরী, গীতাদি, বিজয়া—সকলেই ও বেলায় রং মাখাতে এসেছিল ফুলরেণুকে। তখনই বলে গিয়েছিল : মেয়েদের ও-বেলায় ‘মিলনে’ পাঠিয়ে দিও, আভাদি বলে দিয়েছেন।
হোস্টেল ফাঁকা। ঝি বামুনরাও বোধ হয় সকলে নেই। ঘরদোর বারান্দায় এখনও রং লেগে আছে, আবিরের গুঁড়ো জমে রয়েছে। কেমন একটা গন্ধ ভাসছে বাতাসে। ফুলরেণুকে স্নান করতে হয়েছে মাথা ঘষে, আবিরের ধুলোবালি এখনও যেন মাথায় কিচকিচ করছে, চোখ মুখ গাল গলা খসখসে লাগছে, বেশ একটু উষ্ণও যেন। আজ আর চুল বাঁধা হয়নি, রুক্ষ এলোচুলে একটা গিট দিয়ে নিয়েছে ফুলরেণু। সাদা খোলের শাড়ি পরেছে, পাড়টা চওড়া, সোনালি রং পাড়ের, গায়ের জামাটাও সাদা, চিকনের কাজ করা।
সন্ধের দিকটায় আর ঘরে থাকতে ইচ্ছে করল না। চুপচাপ নিস্তব্ধ হোস্টেল, রান্নাঘরে ঝি-বামুনে রান্নাবান্না করছে। নীচে এসে মাঠে ফুলরেণু ঘুরে বেড়াচ্ছিল। কী পরিষ্কার ঝকঝকে জ্যোৎস্না, পূর্ণিমার মস্ত চাঁদ মাথার ওপর, বাতাসটা এত সুন্দর যে গা-মন জুড়িয়ে যাচ্ছিল। ফুলরেণু গায়ের আঁচল বাতাসে উড়িয়ে মাঠে পায়চারি করছিল, মেয়েরা নেই, কেউ তার আঁচল ওড়ানো, মাথার এলোচুল দেখছে না। কাশীর কথা মনে পড়েছিল মাঝে মাঝে। মা চিঠি দিয়েছে ; টোকনও চিঠি দিয়েছে। টোকনের চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে ; বাড়িতে তাকে নিয়ে রহস্যময় কিছু হচ্ছে। কী হচ্ছে ফুলরেণু অনুমান করতে পারে। টোকন লিখেছে ; ফুলদি, তুই এলে তোর কাছে—মানে সিলেকশান বোর্ডের চেয়ারপার্সনের কাছে ‘ফর সিলেকশন’ ফাইলগুলো দেওয়া হবে।’…টোকনটা বড় ফাজিল হয়ে উঠেছে আজকাল। ফুলরেণুর নিজের ভাই-বোন নেই, মামাতো ভাইবোনরাই সব।
গেট খোলার শব্দ হল। ফুলরেণু অন্যমনস্কভাবে তাকাল। কে যেন আসছে। তারপর খেয়াল করে তাকাতেই যেন অবাক হয়ে গেল। স্বর্ণকমল, স্বর্ণকমল এ সময় কেন ? আজ তার আসার কি দরকার ?
কোঁচা দুলিয়ে, চুড়িদার সাদা দুধের মতন পাঞ্জাবিতে চাঁদের আলো মাখিয়ে কার্তিক ঠাকুরের মতন লোকটা আসছে। ফুলরেণু তাড়াতাড়ি নিজের উড়ন্ত আঁচল সামলে নিল।
স্বর্ণকমল কাছে এসে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে হাসল। ফুলরেণু অবাক গলায় বলল, “কি ব্যাপার ? আপনি ?”
“এলাম।” স্বর্ণকমল হাসিহাসি মুখে বলল।
“আজ কী ? আজ তো দোল। মমতারা কেউ নেই।”
“আপনি আমায় শুক্রবার সন্ধেবেলায় দেখা করতে বলেছিলেন।”
আজ অবশ্য শুক্রবার, এবং সময়টাও সন্ধে। তা বলে লোকটা একেবারে দিনক্ষণ মেপে আসবে। যখন বলেছিল…ফুলরেণু তখন কি অত ভেবে বলেছিল, নাকি তার খেয়াল ছিল শুক্রবার দোল। মমতাদের পড়াতে আসবে যেদিন সেদিন এলেই চলত।
ফুলরেণু সে রকমই ভেবেছিল।
বিরক্ত হয়ে ফুলরেণু বলল, “তা বলে আপনি দোলের দিন সন্ধেবেলায় আসবেন। আজ কি মেয়েরা পড়ে ?”
“তা তো বলেননি আপনি”—স্বর্ণকমল বিনয় করে বলল, “মেয়েদের পড়াব বলেও আমি আসিনি। দেখা করতে বলেছিলেন তাই এলাম। আপনার সময়ের তো দাম আছে। অন্য সময়…”
বাধা দিয়ে ফুলরেণু বলল, “আপনার সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান থাকা উচিত ছিল।”
“আজ্ঞে হ্যাঁ, তা ঠিক।”
ফুলরেণু কি বলবে আর বুঝতে পারল না। লোকটা কি ইচ্ছে করেই এ সময় এসেছে ? ভীষণ চতুর তো ! কিছুই বলা যায় না। এখন কি করবে ফুলরেণু ? স্বর্ণকমলকে তাড়িয়ে দেবে ? অন্যদিন দেখা করতে বলবে ! ফুলরেণুর মনে হল, সেটা বড় বেশি অসভ্যতা এবং অভদ্রতা হবে। হাজার হোক এভাবে আজকের দিনে কাউকে তাড়ানো যায় না।
দাঁড়িয়ে থাকা অস্বস্তিদায়ক। ফুলরেণু পা বাড়াল। শাড়ির আঁচলটা বাঁ হাতে ধরে রেখেছে। স্বর্ণকমলও পাশে পাশে হাঁটতে লাগল।
ফুলরেণু বলল, “ও ব্যাপারে আমি এখনও কিছু ভেবে দেখিনি। সময় পাইনি।”
স্বর্ণকমল বিন্দুমাত্র বিরক্ত হল না, বলল, “তাতে কি ! পরে ভেবে দেখবেন।”
ফুলরেণু বলার মতন আর কিছু পেল না, পায়চারি করার মতন হাঁটতে লাগল নীরব ; স্বর্ণকমলও পাশে পাশে হাঁটছে।
“মেয়েরা সব—কি বলে যেন—পূর্ণিমা মিলনে গেছে…” ফুলরেণু শেষে বলল, চুপচাপ থাকলে এই সময় অন্যরকম মনে হচ্ছে, অস্বস্তি বোধ করছে সে।
“হ্যাঁ, আজ দুর্গাবাড়িতে ‘মিলন’। দোলের দিন প্রতি বছরই হয়। এখানকার বাঙালিরা করে।”
“আপনি গেলেন না।”
“এখানে এলাম।”
ফুলরেণু বলতে যাচ্ছিল : এখানে কি ‘মিলন’ হচ্ছে ? বলতে গিয়েও কোনও রকমে বেফাঁস কথাটা সামলে নিল। নিয়ে যেন ঢোঁক গিলল। মনে মনে রাগল সামান্য।
স্বর্ণকমল চোরা চোখে ফুলরেণুকে দেখছিল। ফুলরেণুর গায়ের রং উজ্জ্বল শ্যাম, মুখটি লাবণ্যভরা। যেন বেলআটা মাখানো। বয়স বেশি না ফুলরেণুর, বছর চব্বিশ পঁচিশ ; সর্বাঙ্গে পুষ্টতা এবং শ্ৰী আছে। ফুলরেণুর মুখে ভাবে ভঙ্গিতে যে গাম্ভীর্য আছে তা কিছুটা কৃত্রিম, কিছুটা যেন কোনও সংস্কার বা গোঁড়ামি বলে…ফুলরেণুকে আজ আরও সুন্দর দেখাচ্ছিল, একমাথা রুক্ষ এলো চুল, বেলফুলের মতন মুখটি যেন ফুটে আছে। চোখের পাতা বন্ধ করে স্বর্ণকমল নিশ্বাস নিল দীর্ঘ করে। নিশ্বাসে শব্দ হল।
ফুলরেণু মুখ ফিরিয়ে তাকাল। কি শুকছে লোকটা ! ফুলরেণু অবাক হয়ে বলল, ‘কী ?”
“কিসের…?”
“ও-রকম করলেন যে !”
“বেশ একটা গন্ধ পেলাম।” স্বর্ণকমল মুখ উঁচু করে নাক টানতে লাগল। “কিসের গন্ধ ?”
“ফুলের—”, স্বর্ণকমল মনে মনে হাসল। ফুলরেণু যেন বাতাসে গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করল, কোনও গন্ধ পেল না। বাতাসটা অবশ্য চমৎকার লাগছিল। মাঠের চারপাশে তাকাল, অনেকটা দূরে করবী গাছের একটা ঝোপ ছাড়া কোথাও কোন গাছ নেই।
ফুলরেণু বলল, “এখানে আবার ফুল কোথায় ?”
স্বর্ণকমল মনে মনে বলল : আমার সামনে : মুখে বলল, “বসন্তকাল—, পবনঃ সুগন্ধি।”
ফুলরেণু আড়চোখে তাকিয়ে স্বর্ণকমলকে দেখল একবার। তারপর মুখ নিচু করে হাঁটতে লাগল। মাঠের কোথাও কোথাও রং শুকিয়ে আছে, কোথাও বা আবির পড়ে আছে ধুলোয় ; মেয়েরা সকালে দৌড়োদৗড়ি করে রং খেলেছে মাঠে। ফুলরেণু মুখ উঠিয়ে সামনে তাকাল, তারপর আকাশের দিকে চোখ তুলল : টলটল করছে পুর্ণিমার চাঁদ।
স্বর্ণকমল বলল, “বেশ লাগছে না ?”
ফুলরেণু কোনও জবাব দিল না।
স্বর্ণকমল আবার বলল, “আহা সেই বসন্তবর্ণনাটি মনে পড়ছে : দুমাঃ সপুষ্পা সলিলং, সপদ্মং, স্ত্রিয়ং সাকামাঃ পবনঃ সুগন্ধ…”
শ্লোকটা শেষ করতে দিল না ফুলরেণু। প্রায় ধমকে উঠে বলল, “আমার সামনে সংস্কৃত বলবেন না।”
“কেন, কেন ?” স্বর্ণকমল যেন খুব অবাক।
“আমি পছন্দ করি না।”
“ও !…কিন্তু এটা কালিদাসের বসন্ত বর্ণনা…”
“কালিদাস…।” ফুলরেণু যেন আঁতকে উঠল। মুহূর্ত কয়েক আর কথা বলতে পারল না, তারপর বলল, “অত্যন্ত অসভ্য, ভালগার।”
স্বর্ণকমল দাঁড়িয়ে পড়ে আবার হাঁটতে লাগল। “আজ্ঞে এর মধ্যে কোনও ভালগারিটি নেই। শুনুন না—‘রম্য-প্রদোষ সময়ঃ স্ফুটচন্দ্রহাসঃ পুংস্কোকিলস্য বিকৃতঃ পবনঃ সুগন্ধি’,…মানে হল—রমণীয় সন্ধ্যাকাল, বিমল চন্দ্রকিরণ, পুংস্কোকিলের কুজন, সুগন্ধি বায়ু…”
“আপনি থামুন, মানে বলতে হবে না”, ফুলরেণু আদেশের মতন করে বলল।
স্বর্ণকমল থামল।
ফুলরেণু বলল, “কলেজে ছেলেমেয়েদের সংস্কৃত পড়ানো বন্ধ করে দেওয়া উচিত। আমি হলে করতাম। …যত সব কুশিক্ষা হচ্ছে।”
“আজ্ঞে—কুশিক্ষা !”
“আপনার কি ধারণা সুশিক্ষা হয় ?”
“না, মানে—, এটা তো রস অনুভবের ব্যাপার।”
“বেশি রসে স্বাদ তেতো হয়।” ফুলরেণু ঠোক্কর দিয়ে বলল। “এখানকার ছেলেমেয়েদের তো দেখছি—কী রকম সব তেতো হয়ে গেছে। যত অসভ্যপনা, বেয়াড়াপনা, বাঁদরামি শিখেছে।”
স্বর্ণকমল নিরীহ ভালমানুষ মতন মুখ করে বলল, “আপনি কি বলতে চাইছেন এদের চিত্ত-প্রকৃতি তরল ও চঞ্চল হয়ে উঠছে।”
“আপনার ওসব ছলছল ভাষা আমি বুঝি না। আমি বলছি এরা বাঁদর হয়ে উঠছে, অভব্য অশালীন হয়ে উঠছে।”
“সংস্কৃত পড়ে ?”
“আপনাদের কাছে ওইসব ছাইভস্ম পড়ে।”
“আপনি যে কোথায় ভস্ম পাচ্ছেন আমি বুঝছি না।…তবে হ্যাঁ, বলতে পারেন ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি ! দু একটা যদি পড়ে দেখতেন ?”
“পড়েছি—পড়েছি।” ফুলরেণু অধৈর্য হয়ে বলল।
“পড়েছেন ! বাঃ !” স্বর্ণকমল পুলকিত বোধ করল। “আরও পড়ুন—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ুন কুমারসম্ভবম্ রঘুবংশম্ অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ মেঘদূতম্…আহা এ-সবের কি তুলনা আছে। অতুলনীয়। যদি বলেন বাংলা মানে দেওয়া বই আমি দিতে পারি।”
“থাক আমার দরকার নেই।” গম্ভীর হয়ে ফুলরেণু বলল। “সে কষ্ট আপনাকে করতে হবে না।”
“কষ্টের কিছু না। এখানেই আছে। মমতার কাছে। আমি চেয়ে নিয়ে দেব। আপনিও চেয়ে নিতে পারেন।”
“আমার চেয়ে দরকার নেই।… আমি জানি কী আছে।” ফুলরেণু গলা চড়িয়ে চোখের দৃষ্টি আগুন করে বলল। “যত ট্রাশ অসভ্যতা ! আপনাদের মতন লোকের এই সবেই মজা।”
‘আজ্ঞে…’ স্বর্ণকমল করজোড়ে বলল, “অপরাধ নেবেন না, একটা কথা বলি : উদেতি পূর্বং কুসুমং ততঃ ফলং ঘনোদয়ঃ—আগে পুষ্পেদগম পরে ফল, আগে জলোদয় পরে বর্ষণ—এই তো নিয়ম। আপনি পড়ে যান পুষ্পেদগম হচ্ছে ধীরে ধীরে পরে ফল হবে ; মেঘের উদয় আমি দেখছি বর্ষণ পরে হবে…”
ফুলরেণুর আর সহ্য হল না। লোকটা তার সঙ্গে রসিকতা করছে ! তামাশা ! কী সাহস দেখেছ ? ফুলরেণু সোজা গেট দেখিয়ে দিল, “আগে আপনি যান পরে অন্য কথা।”
স্বর্ণকমল হেসে ফেলল। ফুলরেণুকে চোখ ভরে দেখতে দেখতে বলল, “যাচ্ছি। আজ দোল পূর্ণিমা, আপনাকে তো হাতে করে আবির-কুঙ্কুম দিতে পারলাম না, প্রশস্তি লেপন করে যাই। সত্যি আপনাকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে আজ।…কালিদাস যে এই বসন্ত ঋতুতে অনঙ্গদেবকে বহুরূপে রমণীদেহে অবস্থান করতে দেখেছেন, তা যথার্থ। আমিও, দেখছি—নেত্রেষু লোলো মদিরালসেষু গণ্ডেষু পাণ্ডুং কঠিনঃ স্তনেষু…আপনার মদিরালস চক্ষুতে চঞ্চলভাবে, গণ্ডদেশে পাণ্ডুরূপে সেই দেবতা বিরাজ করছেন…” বলতে বলতে স্বর্ণকমল গলার স্বর অতি নিচু করল, এবং শেষ শব্দের ব্যাখ্যাটা অশ্রুতভাবে নিজের কাছেই করল ! আর দাঁড়াল না, পালাল।
রাগে ফুলরেণুর সর্বাঙ্গ কাঁপার কথা, মাথায় আগুন জ্বলে ওঠার কথা, কিন্তু বেচারি হঠাৎ কেমন লজ্জায় অস্বস্তিতে আরক্তিম হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। এবং তার বুক কি কারণে যেন কাঁপল।
পাঁচ
দেখতে দেখতে দেড় দু মাস কাটাল। গরমের ছুটিতে ফুলরেণু কাশীতে নিজের বাড়িতে এল। মা বললেন, “আমি কত ভাবনায় ভাবনায় মরতুম, কি জানি কেমন থাকিস। তা বলতে নেই রেণু, তোর শরীর বেশ সেরেছে। মুঙ্গেরের দিকে জলহাওয়া খুব ভাল, না রে ?…” ফুলরেণু শুধু হাসল, কিছু বলল না।
রাত্তিরে টোকন এসে হাতে একটা মস্ত খাম দিল। বলল, “নে ফুলদি, তোর ফাইল। পাঁচজন ক্যান্ডিডেট আছে। তাদের ফটো, নাম ধাম বয়েস প্রফেশন—সমস্ত পার্টিকুলার নোট করে দিয়েছি। এখন তুই বাবা তোর পছন্দমত বেছে নে। …ব্যাপারটা কিন্তু বর্ষায় সারতে হবে, আষাঢ় মাসে।’’
ফুলরেণু হাসল। “বড় ফাজিল হয়ে গিয়েছিস।”
“ফাজিলের কি, বিজনেস ইজ বিজনেস। তোর পর আমি লাগাব।…যাকগে, শোন—ওই পাঁচটা একেবারে পঞ্চপাণ্ডব—ডাক্তার, এঞ্জিনিয়ার, ল’ ইয়ার, ব্লাকমার্কেটিয়ার অ্যান্ড প্রফেসার।”
“প্রফেসার কী রকম প্রফেসার? শুধু প্রফেসার না ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার প্রফেসার?” ফুলরেণু হাসল।
“সব দেখতে পাবি। আমি চলি, একটা নেমন্তন্ন আছে।”
টোকন চলে গেলে ফুলরেণু বিছানায় শুয়ে খানিকটা সময় গড়াগড়ি দিল। বেশ লাগছে। তার হাসি পাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত উঠে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে এসে খাম খুলল। ডাক্তার পাত্র একেবারে গজকচ্ছপ টাইপের, বয়েস আটত্রিশ। বোগাস। এঞ্জিনিয়ার সাহেব একেবারে হাতুড়ি মার্কা, লিডসের ডিপ্লোমা পেয়েছে। রাবিশ। ল’ ইয়ারকে দেখেই নাক কুঁচকে নিল ফুলরেণু, ইয়ারমার্কা মুখ। যাচ্ছেতাই একেবারে ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার—অর্থাৎ বিজনেসম্যান। ওরে বাবা, এ যে বাঘ-ছালের ওপর পা দিয়ে ফুলসাইজের ফটো তুলিয়েছে, চেহারাটা শিকারি ধরনের, গোঁফটা কী বাহারি! দূর দূর! শেষে প্রফেসার মশাইয়ের ছবি বেরুল। এ যে স্বর্ণকমল। ফুলরেণু ছবিটা হাতে নিয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর পাটিকুলার্স দেখল। কী রকম শয়তান, কোথাও দীপনারায়ণ কলেজের নাম দেয়নি, কলেজে পড়ায় এই পর্যন্ত উল্লেখ আছে। অবশ্য স্বর্ণকমলের কোনও দোষ নেই, ফুলরেণুই বলে দিয়েছিল: “আমি জানি না, তোমাদের বাড়ির তরফ থেকে কাউকে দিয়ে লিখিয়ে চিঠি দিও ; তবে মা টোকন যদি জানতে পারে আমার কলেজে তুমি পড়াও তবে আমি সিলেকশান করব না, তা বলে দিচ্ছি কিন্তু।”
স্বর্ণকমলের ছবিটা নিয়ে ফুলরেণু বিছানার মধ্যে গড়াগড়ি খেল, অনেকক্ষণ হাসল, কত কথা ভাবল, শেষে ঘুমিয়ে পড়ে স্বপ্ন দেখ: হোস্টেলে তার ঘরে বসে স্বর্ণকমল তাকে মেঘদূত পড়াচ্ছে: চুড়াপাশে নবকুরবকং…কর্ণে শিরীষং…
দিন তিনেক পরে স্বর্ণকমলের চিঠি এল। মস্ত চিঠি।
মা বলল, “কার চিঠির?’’…ফুলরেণু অন্যদিকে মুখ করে যেতে যেতে বলল, “কলেজের উমাদিটুমাদির হবে।”
বিকেল এবং সন্ধেটা চিঠি পড়ে পড়েই কাটল। বার বার পড়ল ফুলরেণু। যত পড়ছিল ততই বুকের মধ্যে কষ্ট হচ্ছিল, আবার আনন্দেও কেমন অবশ হয়ে পড়ছিল, থেকে থেকে নিশ্বাস ফেলছিল।
রাত্রে বিছানায় শুয়ে দরজা বন্ধ করে ফুলরেণু চিঠির জবাব লিখতে বসল। লেখার প্যাডে কালির আঁচড় আর পড়ে না। যাও বা পড়ে মনে হয় এমন চিঠি সে মাকে লিখেছে, টোকনকে লিখেছে ; এ চিঠি স্বর্ণকমলের বেলায় অচল। পাতাটা ছিঁড়ে ফেলে আবার ফাউন্টেন পেন দাঁত দিয়ে কামড়াতে থাকে ফুলরেণু। এইভাবে অনেকটা রাত হল, অনেকগুলো প্যাডের ফিনফিনে পাতা নষ্ট হল অথচ চিঠি লেখা হল না। ফুলরেণুর কান্না পেতে লাগল। এতদিন সে কেমিস্ট্রির শ শ’ পাতা নোট লিখিয়েছে ; সে সোডিয়াম কার্বোনেটের বিবরণ লিখতে পারে, অক্লেশে নাইট্রোজেন প্রবলেম সম্পর্কে বারোটা পাতা ঝড়ের মতন লিখতে পারে, এখুনি ক্রিস্টাল, সিমেট্রি—তাও পারে কিন্তু হায় হায়—ভালবাসার একটা চিঠি লিখতে পারে না। এই সহজ কাজটা এত শক্ত কে জানত?
শেসে ফুলবেণু উঠল। ঘরের একপাশ থেকে তার সুটকেস টেনে নামিয়ে খুলল। তারপর শাড়ি জামা হাতড়ে সুটকেসের তলা থেকে মৃদুলার খাতার মধ্যে পাওয়া সেই চিঠিটা বের করে বিছানায় নিয়ে এল। বালিশে বুক রেখে ফুলরেণু এবার চিঠি লিখতে বসল। মৃদুলার সেই চিঠি একপাশে খোলা, ফুলরেণু ফাউন্টেনপেনের ঢাকনা খুলে মৃদুলার চিঠি দেখে দেখে—অবিকল সেইভাবে সেই একই ভাষায়—চিঠির নকল করতে লাগল।
পঁচিশ বছর বয়েসে ফুলরেণুর হৃদয় মৃদুলার চিঠির বয়ান অনুযায়ী ময়ূরের মতন নাচতে লাগল, বাতাসের ঝাপটা দিতে লাগল, চাঁদের আলোয় ভরে উঠল। “চোখের পাতা বুজলে তোমায় দেখছি, চোখ খুললেও তুমি। তুমি আমার কাছে সব-সময় আছ, আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছ। কী আনন্দ যে হচ্ছে আমার! তোমার মুখ তোমার হাসি আমি এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারছি না ‘ রাত্তিরে শুতে এসে ঘুম আসছে না, এপাশ ওপাশ করছি, বাইরে সব ঘুমিয়ে পড়েছে এ সময় তুমি কাছে থাকলে সব চাওয়া পূর্ণ হত। তুমি নেই তাই বালিশের কানে কানে তোমায় আমার কথা বলছি! তুমি কি শুনতে পাচ্ছ?”…এই সমস্ত মৃদুলার চিঠিতে যা ছিল, যেমন ছিল লিখল ফুলরেণু। এবং চিঠির শেষে মৃদুলার চিঠির মতনই লিখল, “তুমি আমার আদর নিও।” মৃদুলার চিঠিতে তলায় নাম ছিল না। ফুলরেণু নিজের নাম দিল। দিয়ে চিঠিটা আড়াগোড়া পড়ে আনন্দের আবেশে ঘুমিয়ে পড়ল।
ছয়
বিয়ের পর ফুলশয্যার দিন পাশাপাশি শুয়ে গল্প করতে করতে স্বর্ণকমল বলল, “ফুল, কাশী থেকে তুমি আমায় প্রথম যে চিঠিটা লিখেছিলে সেটা স্রেফ ‘টুকলি’।”
“টুকলি?” ফুলরেণু চমকে উঠে বালিশ থেকে মাথা সরিয়ে উঠে পড়ে আর কি।
“তুমি নিজে লেখোনি।”
“মানে!…”
“ওটা—মানে ওই চিঠিটা একটা বইয়ে আছে।”
“বই!” ফুলরেণু অপ্রস্তুতের একশেষ। কিন্তু মৃদুলার খাতার মধ্যে যে ছিল চিঠিটা। কেমন সন্দেহ হল ফুলরেণুর। বলল, “তুমি জানলে কী করে!”
“জানলাম।”
“এমনি এমনি জেনে গেলে!”
“না না, এমনি কেন! বইটা আমার কাছে ছিল।” স্বর্ণকমল হাসছিল। “খুব পপুলার বই। প্রেমপত্র সংকলন।”
“ইয়ার্কি! তোমার মতন অসভ্য নাকি সবাই, যে নিজেদের কীর্তি ছাপাবে।!”
“আরে না, কীর্তি ছাপাবে কেন। বাংলা গল্প উপন্যাস থেকে বাছাই করে নেওয়া চিঠি। প্রেমপত্র।”
“বইটা আছে তোমার?”
“এখন আর পাচ্ছি না। কে যে পড়তে নিয়ে চুরি করে নিল! সকলেরই দরকার পড়ে তো!” বলে হেসে ফুলরেণুর হাত ধরে বুকের ওপর টেনে নিয়ে বলল, “তুমিই চুরি করেছিলে নাকি? তুমি যা চোর। ইউ আর এ টুকলি।”
স্বর্ণকমলের বুকে লজ্জায় মুখ রেখে কিছুক্ষণ পড়ে থাকল ফুলরেণু। তারপর মুখ ঘুরিয়ে স্বর্ণকমলের কানের দিকে ঠোঁট নিয়ে বলল, “আর তুমি যে আমার প্রশস্তি গাইতে, মন ভোলাতে সেও তো তোমার কালিদাসের টুকলি। তুমি চোরের বেশি বাটপাড়।”
স্বর্ণকমল হেসে ফেলল, হাসতে হাসতে বলল, “এ সব চুরিতে দোষ নেই।…কি বল।”
ফুলরেণু পিঁপড়ের মতন নিশব্দে স্বর্ণকমলের কানের লতি কামড়ে দিল।
গোরাচাঁদ
গোরাচাঁদ ঘরে আসতেই বন্ধুরা তাকে সহর্ষে অভ্যর্থনা জানাল। আয় গোরা, আয়; একটু আগেই তোর কথা হচ্ছিল। হপ্তাখানেক দেখা নেই—ভাবছিলাম হল কী! জলধর কালই তোর বাড়ি যেত। তা তোর বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল?
বন্ধু বলতে ঘরে তখন তারা চারজন। সলিল, জলধর, নিয়োগী আর মানিক। ওরা তাস খেলছিল। বেশির ভাগ দিন সন্ধেটা ওদের তাস খেলেই কেটে যায়। সলিলদের বাড়ির বৈঠকখানার নামই হয়ে গিয়েছে ‘তাসের ঘর’।
গোরাচাঁদ খুবই বিমর্ষচিত্তে ঘরে ঢুকেছিল। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল, জবরদস্ত ডেঙ্গুজ্বর কিংবা ম্যালেরিয়ায় ভুগে সবে বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে। চোখমুখ শুকনো, মাথার চুল উস্কোখুস্কো, দাড়ি কামানো হয়নি ভাল করে, চোখের চশমা ঢিলে হয়ে নাকের ডগা পর্যন্ত গড়িয়ে এসেছে। এরকম হবার কথা নয়, অন্তত এখন।
হাতের তাস হাতে রেখেই জলধর বন্ধুকে দেখছিল। বলল, “কিরে গোরা, তোর এ হাল কেন? অসুখ-বিসুখ করেছিল নাকি? আমার বাড়ির ফোনটা ডেড, নয়ত তোকে—।”
গোরাচাঁদ কোনও কথা বলল না। একেবারে কোণের দিকে গিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল।
নিয়োগী বলল, “বিয়ে পেছিয়ে গেল নাকি রে? মন খারাপ? আরে মন খারাপ হবার কী আছে! গরমে বিয়েটা ঠিক জমে না। গরম বর্ষা পার করে দে—মাত্তর তো আর চার পাঁচটা মাস, তারপর লাগা। অর্লি অঘ্রানে। নরম শীতে নতুন বউ…ফাইন!”
গোরাচাঁদ বেশ বিরক্ত হয়ে নিয়োগীকে দেখল। তারপর হাত বাড়িয়ে বলল, “জলের বোতলটা দে।”
বন্ধুরা তাস খেলতে বসলে চায়ের কাপ খাবারের প্লেটের সঙ্গে কয়েকটা জলের বোতলও জমে যায়।
মানিক জলের বোতল এগিয়ে দিল। বলল, “খালি পেটে জল খাবে দাদা? একটু তলানি আছে। দেব?” বলে হাসল। বন্ধুদের মধ্যে মানিক হল জুনিয়র।
গোরাচাঁদ ও-সব নেশার জিনিস খায় না। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে একবার দশ বিশ ফোঁটা খেয়েছিল। মিলিটারি মাল। তাতেই তার জিব জড়িয়ে গিয়ে সে কী অবস্থা! পান সিগারেট ছাড়া গোরাচাঁদের আর কোনও নেশা নেই। তার বন্ধুরাও ঠিক নেশুড়ে নয়, তবে মাঝেমাঝে দু-এক পাত্তর চড়িয়ে নেয়।
জল বেশি ছিল না। যেটুকু ছিল খেয়ে নিল গোরাচাঁদ। তারপর বলল, “একটু চা হলে হত।”
সলিল বলল, “চা হবে। আগে বল, তোর হয়েছে কী?”
“সে অনেক কথা। বলছি। আগে একটু চা…।”
সলিল উঠে গেল চায়ের কথা বলতে।
জলধর বলল, “আমরা তো তোর বিয়ে নিয়েই কথা বলছিলাম। ভাবছিলাম তোকে বলব, তোর জেঠামশাই ওল্ডম্যান, তাঁকে আর কষ্ট দেওয়া কেন! তোর বিয়ের ব্যাপারটা আমরাই ম্যানেজ করে দেব। এই ধর বিয়ের চিঠি, প্যান্ডেল, খাওয়া-দাওয়া, লোকজনকে আপ্যায়ন…।”
জলধরের কথা শেষ হল না, গোরাচাঁদ বলল, “বিয়ে হচ্ছে না। আমি করছি না। ”
বন্ধুরা সমস্বরে বলে উঠল, “সে কি রে? কেন? সব ঠিক হয়ে গেল—এখন— ?”
সলিল ফিরে এল।
সলিল ফিরে আসতেই মানিক বলল, “সলিলদা, শোনো গোরাদা কী বলছে! বিয়ে করছে না গোরাদা।”
সলিল দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল গোরাকে। অবাক হয়ে বলল, “বলিস কিরে! সত্যি নাকি?”
গোরাচাঁদ মাথা নেড়ে বলল, “হ্যাঁ। এই বিয়ে করছি না।”
“কেন?”
“আমাকে বিচ্ছিরিভাবে ইনসাল্ট করেছে। যা-তা বলেছে মেয়েটা।”
“মেয়েটা! কোন মেয়েটা?”
“ওই মেয়েটা, কমলিকা না মালবিকা— কী যেন নাম ওটার।” গোরাঁচাদ রীতিমতন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের গলায় বলল। নামটাও যেভাবে বলল—মনে হল,ওই মেয়ের নাম মনে রাখারও যেন তার প্রয়োজন নেই।
তাস খেলার পাট চুকে গেল। হাতের তাস ফেলে বন্ধুরা পরম কৌতুহলে গোরাচাঁদকে দেখতে লাগল। ব্যাপারটা তাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছিল। গোরাচাঁদ কোনও কালেই বদমেজাজি নয়, হঠকারিও নয়। রুক্ষ রূঢ় সে হতে পারে না কোনও অবস্থাতেই। ওর স্বভাব নরম। নিরীহ ভিতু ধরনের মানুষ। সাদামাটা সরল। তার জেঠামশাইয়ের একান্ত বাধ্য ও অনুগত। অবশ্য তার কারণ আছে। গোরাচাঁদের বাবা যখন মারা যান গোরার বয়েস তখন তিন। জেঠামশাই জেঠাইমাই তাকে মানুষ করেছেন।
মা অবশ্য ছিলেন। কিন্তু ওর তেরো চোদ্দো বছর বয়েসে মা-ও চলে যান। জেঠামশাই জেঠাইমাই তার সব। জেঠামশাইদের কোনো ছেলে নেই, একটি মেয়ে আছে—গোরাচাঁদের দিদি। দিদিও অনেক দিন ধরে অন্য সংসারের লোক হয়ে গিয়েছে—থাকেও কলকাতার বাইরে। দুর্গাপুরে। মাঝেমধ্যে আসে অবশ্য। দিদিও গোরাচাঁদকে ভালবাসে খুব। …তা ছেলে হিসেবে গোরাচাঁদ চমৎকার। সরল, ভদ্র , সভ্য, নম্র। দেখতেও ভাল। গায়ের রং ফরসা ; চেহারা গোলগাল। চোখ দুটি বড় বড় মুখে সব সময় একটু হাসি লেগে থাকে।
বন্ধুরা যেন বুঝতে পারছিল না, শিষ্ট মার্জিত নম্র গোরাচাঁদ হঠাৎ এভাবে বিগড়ে গেল কেন? ও কি সত্যিই বিগড়েছে? না, তামাশা করছে? চেহারা দেখে তো মনে হয় না তামাশা করছে!
জলধর যেন তখনও বিশ্বাস করেনি। বলল, “তুই বেটা সত্যি বলছিস? না, নাটক করছিস?” বলে বন্ধুদের সঙ্গে একবার চোখাচুখি করে নিল।
“সত্যি বলছি।”
“হয়েছেটা কী?”
“বললাম তো, মেয়েটা আমাকে ইনসাল্ট করেছে। একবার নয় অনেকবার। কালও আমাকে যা-তা বলেছে।”
“কেন?”
“আমি কেমন করে জানব?”
“তুই কিছু করেছিলি?”
গোরাচাঁদ আরও বিরক্ত হল। বলল, “আমি কিছু করব? মানে? আমি তাকে চোখেই দেখিনি। সে তুই দেখেছিস।”
কথাটা মিথ্যে নয়। সম্বন্ধ-করা বিয়ে। জেঠামশাইয়ের এক বন্ধু সম্বন্ধটা দিয়েছিল। জেঠামশাই জেঠাইমা দিদি মেয়ে দেখেছে। আর গোরাচাঁদ ও তার বন্ধুদের তরফে দেখেছে জলধর।
মানিক রঙ্গ করে বলল, “চোখে দেখনি বোলো না দাদা, বলো ফটো দেখেছ—ফেস টু ফেস হওনি।”
সলিল বলল, “এই মানিক, চুপ কর। ব্যাপারটা শুনতে দে।” বলে গোরাচাঁদের কাছাকাছি গিয়ে বসল। “ব্যাপারটা একটু খোলসা করে বল। হয়েছেটা কী?”
গোরাচাঁদ সামান্য সময় চুপ করে থাকল। বলল, “কী বলব! গত হপ্তায় যখন এখানে এলাম—তোদের বললাম, জেঠামশাই এই জষ্টি মাসেই বিয়ের তারিখ ঠিক করবে বলেছে। মেয়েদের তরফও তাই চায়। জেঠাইমা বলছে, আষাঢ়। জ্যৈষ্ঠমাসে নাকি বড় ছেলের বিয়ে দিতে নেই।”
নিয়োগী বলল, “তোর আর বড় ছোট কী! তুই তো একটাই।”
সলিল বলল, “ছেড়ে দে, যাহা বাহান্ন তাহা তিপান্ন, জষ্টিমাস আর আষাঢ় মাসে তফাতটা কী!… তারপর কী হল বল?”
গোরাচাঁদ বলল, “মাস নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা ছিল না। বিশ্বাস কর। তা গত হপ্তায় এখান থেকে ফিরে গেলাম—সেটা তোর শনিবার। রবিবার সন্ধেবেলায় এক ফোন।”
“ফোন?”
“বাড়িতে। ফোন তুলতেই একটা মেয়ের গলা। কী বলল জানিস?”
“কী?” বন্ধুরা এসঙ্গে বলল।
“বলল, কী গো নদের চাঁদ কেমন আছ?”
“নদের চাঁদ?”
“বিশ্বাস কর, প্রথম কথাই বলল, কী গো নদের চাঁদ, কেমন আছ? আমি ভাই একেবারে হকচকিয়ে গেলাম। বুঝতেই পারলাম না কী ব্যাপার। আজকাল ফোনে যা সব কাণ্ড হয় তোরা জানিস। কিছু চ্যাংড়া আজেবাজে কথা বলে, অসভ্যতা করে। চেংড়িরাও করে ভাই। থার্ড ক্লাস কথাবার্তা বলে। তা আমি বললাম, কাকে চাই? কে নদের চাঁদ?.. তখন মেয়েটা বলল, আহা, ঢং কোরো না। তোমাকেই চাই! গোরাচাঁদ না কালাচাঁদ! কী নাম রে? ভদ্রলোকের ওই সব নাম হয় নাকি? শোনো নদের চাঁদ, বিয়ে করতে সাধ হয়েছে—নামটা পালটাতে পারোনি। যাও কোর্টে গিয়ে এফিডেভিট করে নামটা আগে পালটে নাও। টেলিফোনের পাঁজিতে ভাল ভাল নাম পাবে। বুঝলে? নামের কী বাহার? গোরাচাঁদ! অখাদ্য। আবার করেন কী, না—গেঞ্জি জাঙ্গিয়ার ব্যবসা! ছিছি! ওই ছেলের আবার বিয়ে করতে সাধ! নোলা দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে! লজ্জাও করে না?”
বন্ধুরা অবাক। বিশ্বাস করতে পারছিল না। জলধর বলল, “যাঃ, কী বলছিস! তোকে এসব কথা বলল? একটা মেয়ে? তাও আবার যে-মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা ফাইন্যাল হয়ে গিয়েছে।”
গোরাচাঁদ মাথা নেড়ে সদুঃখে বলল, “শুধু ওইটুকু বলল নাকি! আরও কত কী বলল। অসভ্যের মতন। তারপর আরও বলল, কাল আবার ফোন করব। রাত আটটা নাগাদ। ফোন ধরবে। না ধরলে তোমার বারোটা বাজিয়ে দেব। হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেব—বুঝলে কালাচাঁদ। আমায় তুমি চেনো না।”
সলিল বন্ধুদের মুখের দিকে তাকাল। শেষে গোরাচাঁদের দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাসের গলায় বলল, “গোরা, দিস ইজ নট পসিবল। আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। বিয়ে আমরাও করেছি। আমাদের বউরাও কম তেঁয়েটে নয়। তা বলে তারা বিয়ের আগে এভাবে কথা বলেনি। সে সাহস ছিল না।”
মানিক বলল, “দাদা, তুমি কি ফোন ধরার সময় হুঁশে ছিলে?”
“মানে?”
“মানে নরম্যাল ছিলে তো? কান ঠিক ছিল! তোমার আবার কানের দোষ আছে একটু।”
“বাজে কথা বোলা না।”
নিয়োগী বলল, “গোরা, মেয়েটার গলা শুনে তুই চিনতে পারলি?”
গোরাচাঁদ রেগে গিয়ে বলল, “আমি কি মেয়ের গলা শুনেছি? না, তাকে চোখে দেখেছি।”
“তবে কেমন করে বুঝলি ওই মেয়েটাই ফোন করছে?”
“বাঃ, অদ্ভুত কথা। কেমন করে বুঝলি! মেয়েটা অত কথা বলে যাচ্ছে, হাসছে হি হি করে, টন্ট করছে—আর আমি বুঝব না! আমি কি গাধা! তা ছাড়া ও তো বুঝিয়েই দিল—এই হল সেই মেয়ে যার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছে।”
সলিল বলল, “তুই নাম জানতে চাইলি না?”
“চেয়েছি। বলেছে, ন্যাকামি কোরো না! নাম না বললে চিনতে পারছ না, না?”
জলধর বলল, “সেই মেয়েই। কমলিকা। আমি তো ওকে দেখেছি। কথাও শুনেছি। মেয়েটাকে দেখতে ভাল। তবে ভেতরে বিচ্ছু বলে মনে হল। যে-ভাবে টেরচা চোখে আমাকে দেখছিল। গলার স্বরটা একটু ভাঙা ভাঙা, না কিরে গোরা?”
গোরাচাঁদ বলল, “ভাই, ফোনে গলা শুনে বোঝা যায় না। অচেনা গলা। তবে জোর আছে গলার। ধমক মেরে কথা বলে। “
মানিক বলল, “পরের দিন তোমাকে ফোন করেছিল আবার?”
“করেছিল। আটটার পর পরই।”
কী বলল?”
“ন্যাস্টি কথাবার্তা।”
“অশ্লীল কিছু?”
“নানা, ভালগার টাইপের কথাবার্তা! আমায় কেমন নাড়ু-নাড়ু দেখতে ! চোখ লিচুর মতন, নাক ভুটানিদের টাইপ। আমার নাকি গলগণ্ড রোগ আছে।”
“গলগণ্ড! তোমার? কই আমরা তো দেখছি না। বরং তোমার গল বেশ গোলগাল। তা শুধু চেহারার কথা বলল?”
“চেহারা, স্বভাব। হোয়াট নট! যা প্রাণে চাইছিল বলে গেল। তারপর শেষে বলল, পয়সা ছড়ালে কাকের অভাব হয় না বুঝলে নাড়গোপাল। তোমার মতন পাত্তর আমার পাশে দাঁড়াবার যুগ্যি নয়। আমার বাপ অনেক ভাল ভাল পাত্তর আনতে পারে—ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সিএ, সরকারি অফিসার। তুমি তাদের কাছে গোল্লা। হনুমান!”
“হনুমান?” মানিক আঁতকে উঠল। “দাদা, তোমায় হনুমান বলল! কী মেয়েরে বাবা! এ তো অত্যন্ত অসভ্য, বেয়াদপ!”
এমন সময় চা এল গোরাচাঁদের।
চা দিয়ে বাচ্চা মেয়েটা চলে যেতেই গোরাচাঁদ কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, “কী বলব ভাই! রোজ রাত আটটার পর মেয়েটা ফোন করে আর একতরফা যা মুখে আসে বলে যায়। শেষে কাল বলল, শোনো নদের চাঁদ তোমায় ওয়ার্নিং দিয়ে দিচ্ছি, তুমি যদি গাড়ি সাজিয়ে টোপর হাতে সত্যিই বিয়ে করতে আস, বিপদ হবে। পাড়ার ছেলেদের বলে রাখব, বোমা মেরে তোমার বিয়ের সাধ ঘুচিয়ে দেবে।”
নিয়োগী সভয়ে বলল, “সে কিরে? পাড়ার ছেলেদের লেলিয়ে দেবে বোমা মারতে। এ তো মাইরি পলিটিক্যাল নেতাদের মতন কথা হল! মেয়েটা তো ডেনজারাস।”
গোরাচাঁদ বলল, “আমিও কাল মাথা ঠিক রাখতে পারিনি। স্ট্রেট বলে দিয়েছি—গুঁড়ো মশলার মেয়ে বিয়ে করতে আমার বয়ে গেছে। যত্ত ভেজাল!”
সলিলের যেন রোমহর্ষ অনুভূতি হল। বলল, “তুই বললি?”
“বললাম। কালোকে কালো বলব—তাতে ভয় কিসের! ওরা তো গুঁড়ো মশলার বাড়ির লোক। মেয়ের বাপের গুঁড়ো মশলার বিজনেস। অন্নপূর্ণা গুঁড়ো মশলা! আমাকে যদি ও গেঞ্জি জাঙ্গিয়ার ব্যবসাদারের ছেলে বলতে পারে—আমি ওকে গুঁড়ো মশলা বলতে পারব না? আমাদের সাতাশ বছরের হোসিয়ারি কারখানা। হোসিয়ারি বিজনেসে সুতো ভালমন্দ হতে পারে— কিন্তু ভেজাল চলে না। ওরা ভেজাল। আমরা নির্ভেজাল।
বন্ধুরা প্রথমটায় কথা বলতে পারল না। গোরাচাঁদকে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল।
নিয়োগী শেষমেশ কথা বলল। “গোরা, তুই ঠিক করেছিস। রাইটলি সার্ভড। তোর কারেজ দেখে জয় হিন্দ বলতে ইচ্ছে করছে।”
জলধররা হেসে ফেলল। অবশ্য অট্টহাস্য নয়। মুচকি হাসল।
সলিলদের অ্যাটর্নি অফিস। বাপকাকার আমলের। আইনটা তার মাথায় আসে চট করে। ঠিক আইন নয়, তবে আসল কথাটা সে না বলে পারল না। বলল,”গোরা, কেস তুই কাঁচাতে চাইলেও কি পারবি? তোর জেঠামশাই! বলেছিস তাঁকে?”
গোরাচাঁদ বলল, ভয়ভয় গলায়, “না ভাই, বলিনি। জেঠামশাইকে কি এসব কথা বলা যায়! বিশ্বাসই করবে না। বড় এক বগ্গা মানুষ। তার ওপর ওই গুঁড়ো মশলার সঙ্গে জেঠামশাইয়ের খাতির জমে গেছে। আমি যদি বলি, মেয়েদের বাড়ি থেকে মেয়েটা রোজ রাত্তিরে আমায় ফোন করছে, জেঠামশাই ভাববে, আমি তলায় তলায় ইয়ে করছি। বলবে, রাস্কেল—তুই বললেই আমি মেনে নেব—ও-বাড়ির থেকে মেয়েটি তোকে ফোন করে। বিয়ের আগেই। তুই আমায় সহবত শেখাবি! আসলে তোর কোনো বদ মতলব আছে।”
জলধর মাথা নেড়ে বলল, “ঠিক। জেঠামশাইকে একথা বলা যায় না। বলা উচিত নয়।”
নিগোগী বলল, “তা হলে জেঠাইমাকে বল।”
“জেঠাইমা মানেই জেঠামশাই। বলার সঙ্গে সঙ্গে জেঠার কানে চলে যাবে।”
“তা হলে?”
মনমরা মুখ করে গোরাচাঁদ বলল, “বড়দের কানে উঠলেই—এবাড়ি ওবাড়ি ঝগড়া লেগে যাবে। তারপর ধর হাজার হোক, ওরা মেয়ে পক্ষ! মেয়ের বাপ-মা যখন মেয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে—সে বড় কেলেঙ্কারি হবে। একটা মেয়ের পক্ষে নিজের প্রেস্টিজ বাঁচানো বড় কথা। …না, আমি অতটা অসভ্যতা করতে পারব না। এক আমি দিদিকে বলতে পারি! কিন্তু কোথায় দিদি? সে না আসা পর্যন্ত কিছুই করতে পারছি না।…সত্যি বলতে কি, আমি চাইছি, অন্য রকম কিছু করতে, যাতে এই নেগোসিয়েশানটা নিজের থেকেই ভেঙে যায়। …তোরা আমায় বাঁচা।”
মানিক বলল, “কেমন করে?”
গোরাচাঁদ বলল, “কেমন করে—সেটা তোরা ঠিক কর। তোরা আমার বন্ধু। বন্ধু হয়ে যদি এসময়ে আমায় না দেখিস, কবে দেখবি! আমি তোদের কাছে এসেছি বিপদে পড়ে। যা হয় তোরা কর।”
বন্ধুরা চুপ। কী বলবে! হঠাৎ জলধর বলল, “দাঁড়া, দেখছি। ব্যবস্থা একটা করতেই হবে।”
দুই
মাঝে একটা দিন বাদ গেল। তার পরের দিন গোরাচাঁদ ট্যাক্সি করে এসে হাজির। বাড়ির সামনে ডিজেল ট্যাক্সির বিকট আওয়াজ মিলোতে না মিলোতেই গোরাচাঁদ যেন টলতে টলতে ঘরে ঢুকল। চোখ লালচে, মুখ টকটক করছে, ঘামছিল দরদর করে। জামার বোতাম খোলা। ওকে দেখে মনে হচ্ছিল, কিছু একটা ঘটেছে। গোরাচাঁদের এমন চেহারা বড় একটা দেখা যায় না।
ঘরে এসে গোরাচাঁদ বন্ধুদের তাস খেলা দেখতে দেখতে ক্ষোভের গলায় বলল, “তাস খেলছিস! খেল! সারা জীবন তাসই খেলে যা?”
সলিল বন্ধুকে দেখতে দেখতে বলল, “কেন, কী হয়েছে?”
“না, হবে আবার কী! কিছুই হয়নি। আমি শুধু তোদের দেখছি। তোরা আমার বন্ধু! ভাবতেও কষ্ট হয়। হাউ সেলফিশ!”
নিয়োগী বলল, “কী হয়েছে বলবি তো! ঘরে ঢুকেই হেঁয়ালি শুরু করলি!”।
মানিক হাত বাড়িয়ে কাছে ডাকল। বলল, “দাদা, তুমি বোসো। আগে বোসো।”
“বসব! আমার বসার দরকার নেই! আমি তাস খেলতে আসিনি।”
জলধর বলল, “নতুন কিছু হয়েছে বুঝি? বেজায় খেপে গিয়েছিস?”
গোরাচাঁদ বলল, “খেপে গিয়েছি। খেপে যাওয়া তো সামান্য ব্যাপার ; আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। সারা গা জ্বলে যাচ্ছে! মাথা কেমন করছে!”
সলিল বলল, “বোস আগে। মাথা ঠাণ্ডা কর। জল খা।” বলে পাশ থেকে জলের বোতল বাড়িয়ে দিল।
গোরাচাঁদ জলের বোতল নিল না। বলল, “আমি আর সহ্য করতে পারছি না। মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। আমাকে বাড়ি ছাড়া করাবে ওই মেয়েটা। আমার সুখস্বস্তির বারোটা বাজিয়ে দিল।”
সলিল বলল, “আবার কী হল? এখনও ফোন করছে?”
“কাল করেনি। আজ করেছিল। আমাদের অফিসে। ভাগ্যিস জেঠামশাই তখন ছিল না?”
“কখন করেছিল।”
“এই তো বিকেলের পর, ছ’টা সোয়া ছটা।”
“তুই তা হলে তোদের অফিস থেকেই আসছিস?”
মাথা হেলিয়ে গোরাচাঁদ বলল, “না এসে পারলাম না। তোরা আমার অবস্থাটা যদি বুঝতিস!”
নিয়োগী বলল, “কী বলল মেয়েটা?”
“যা মুখে আসে বলে গেল। আমাকে নিয়ে রগড় করল, টিজ করল। …আমায় কী বলে জানিস? কত বড় আস্পর্ধা! বলল, তোমার যা বুদ্ধি গোরাচাঁদ—ছাগলের মাথাও তার চেয়ে সাফ। টুকেমুকে বি কম পাস করেছিলে, পেছনে তোমার জেঠা এক জোড়া ঠেলা লাগিয়েছিল পয়সা খরচ করে। ওই বুদ্ধি নিয়ে তুমি গেঞ্জির ব্যবসা করবে! যতদিন জেঠামশাই আছে, তারপর তো তোমায় সকলে লুটেপুটে খাবে। তুমিও দু হাতে পয়সা উড়িয়ে রাস্তায় দাঁড়াবে। তোমার যে কত মুরোদ আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি। না আছে বিদ্যে না বুদ্ধি! তোমার মতন অপদার্থকে বিয়ে করে আমি কি শেষে হাঁড়ি মেজে মরব। ওটি হচ্ছে না। “
জলধর বিস্ফারিত বদনে বলল, “বলিস কী! এসব কথা বলল তোকে। ছাগল বলল।”
“ছাগলের চেয়েও খারাপ বলল। …ছুঁচোটুচোও বলল।”
“আর কী বলল?”
“বলল, আমার স্বভাব-চরিত্র খারাপ।”
“স্বভাব-চরিত্র খারাপ?” মানিক হাতের তাস ফেলে দিয়ে থ’মেরে বসে থাকল কয়েক মুহূর্ত। তারপর দু হাতে মুখ ঢেকে মাথা ঝাঁকাতে লাগল। “ওঃ, ভাবা যায় না। দাদার স্বভাব হল ঝরনার জল। স্ফটিক স্বচ্ছ! বিশুদ্ধ, জার্ম ফ্রি, ব্যাকটেরিয়া মাইনাস। এমন স্বভাব লাখে একটাও পাওয়া যায় না। সেই দাদাকে কিনা স্বভাব নিয়ে কথা বলা! ছি ছি! এ তো মানহানির মামলা আনা যায়!”
মানিককে থামিয়ে দিয়ে নিয়োগী বলল, “গোরা, স্বভাবের সঙ্গে চরিত্রও বলল? তোর চরিত্র? মানে ক্যারেকটার?”
গোরাচাঁদ এবার গলা চড়িয়ে বলল, “বলল মানে? এমন একটা খারাপ কথা বলল শুনলে তোরা কানে আঙুল দিবি।”
জলধর গলা বালিয়ে বলল, “কী খারাপ কথা বলল? ইয়ের কথাটথা—?”
“বলল, আমি একটা মেয়ের সব লুটেপুটে নিয়েছি। মেয়েটাকে চিট করেছি। তাকে পথে বসিয়ে এখন দিব্যি সাধুপুরুষ সেজে বিয়ে করতে যাচ্ছি অন্য মেয়েকে। আমি বজ্জাত, বেহায়া, ক্রিমিন্যাল। আমাকে জেলে দেওয়া উচিত।”
সলিল আর নিয়োগী মাথা নাড়তে নাড়তে একসঙ্গে বলল, “দিস ইজ টু মাচ। আর টলারেট করা যায় না।”
মানিক বলল, “দাদা, লুটেপুটে খাওয়া মেয়েটার নাম বলল?” বলে আড়চোখে তাকিয়ে থাকল।
“না।” গোরাচাঁদ প্রায় ধমকে উঠল। “নাম বলবে! কিসের নাম? কার নাম? আমি কি তোমার মতন মেয়ে-হ্যাংলা!…” বলে সলিলদের দিকে তাকাল গোরাচাঁদ। বলল, “আমার ভীষণ লেগেছে, ভাই। জীবনেও এত খারাপ, বাজে, মিথ্যে কথা শুনিনি। ভদ্রলোকের ছেলে একেবারে ইতর হয়ে গেলুম। তোমরা হয় কিছু করো, না হয় বন্ধুত্ব শেষ করে দাও।”
বন্ধুরা চুপচাপ। মুখ নিচু করে বসে থাকল যেন।
শেষে জলধর বলল, “ভাবিস না গোরা, আমি আছি। তোর হয়ে লড়ে যাব। দেখছি মেয়েটাকে। “
তিন
দিন কয়েক পরে গোরাচাঁদ বন্ধুদের আড্ডায় এসে দেখল, নতুন একজনের আবির্ভাব ঘটেছে সেখানে। এ মুখ তার দেখা নয়, চেনাও নয়। তাদের এই আড্ডায় তারা চার পাঁচ জন নিয়মিত আড্ডাধারী ছাড়াও মাঝেমাঝে অনিয়মিত দু একজন গল্পগুজব করতে চলে আসে। তারাও বন্ধুস্থানীয়। কিন্তু এই নতুন মানুষটিকে গোরাচাঁদ কখনও দেখেনি।
গোরাচাঁদকে দেখেই জলধর হাত বাড়িয়ে ডেকে নিতে নিতে বলল, “আয় গোরা, তোর জন্যে হাঁ করে বসে আছি। একটু দেরি করে ফেললি।”
দেরি সামান্য হয়েছিল গোরাচাঁদের। নিয়োগী খবর দিয়েছিল, সাতটা নাগাদ চলে আসবি। জরুরি ব্যাপার আছে।
এখন প্রায় পৌনে আট।
মানিক বলল, “দাদা, তুমি কি রাত আটটার প্রোগ্রাম শেষ করে আসছ?”
গোরাচাঁদ কোনো জবাব দিল না কথার। মানিকটা দিন দিন বড় বেশি চ্যাংড়া হয়ে উঠছে।
জলধর বলল, “গোরা, আলাপ করিয়ে দিই। এ হল আমার পুরনো বন্ধু। চারু ব্যানার্জি। আমরা সিবি বলে ডাকতাম। স্কটিশে আমার ক্লাসমেট ছিল। সিবি এখন ঈগল এজেন্সির পার্টনার।” বলে সিবির দিকে তাকিয়ে আবার বলল, “চারু, এই আমাদের গোরা। এর কথাই তোমাকে বলেছিলাম। বেচারির একেবারে যায়-যায়, অবস্থা। তোমায় কিছু একটা করতেই হবে।”
ঠিক নমস্কার নয়, চোখে চোখে এক রকম আলাপের সৌজন্য বিনিময় হল। চারুর চোখে ঈষৎ হাসি, গোরাচাঁদের চোখে খানিকটা কৌতূহল।
গোরাচাঁদ দেখছিল চারুকে। বেশ টগবগে চেহারা, ধারালো নাকমুখ, গায়ের রং কালচে। চারু গোরাচাঁদেরই সমবয়েসি হবে। গালে পাতলা দাড়ির জন্যে খানিকটা যেন ব্যক্তিত্বময় বলে মনে হয়। হাতে পাইপ।
সলিল বলল, “বোস গোরা, এখানে আয়। তোর কথা জলধর সবই বলেছে সিবিকে। …ফারদার তোর যদি কিছু বলার থাকে বলতে পারিস।”
গোরাচাঁদ বলল, “আমি ঠিক বুঝতে পারছি না… উনি…!”
জলধর বলল, “উনি একজন প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটার। ঈগল পাখি মানে লোকের হাঁড়ির খবর টেনে বার করা ওঁর পেশা। অবশ্য টাকা দিয়ে চারুকে ভাড়া করতে হয়। …তোর কপাল ভাল গোরা, চারুকে আমি পেয়ে গেলাম। একেবারেই হঠাৎ দেখা আমাদের অফিসের সামনে। অনেক কাল পরে। চারু বলল, ও এখন ঈগল এজেন্সিতে কাজ করছে। পার্টনার। ওকে পেয়ে আমি যেন হাতে চাঁদ পেয়ে গেলুম। মনে হল, চারু আমাদের কাজে আসতে পারে। দারুণ হেলপ হবে। তোর কথা বললুম। আজ ওকে আসতে বলেছিলুম এখানে—তোর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। আমরাও সবাই থাকব। ভাল করে সব কথা বলা যাবে।”
গোরাচাঁদ তখনও ভাল করে কিছু বুঝছিল না। বন্ধুদের দেখছিল।
সলিল বলল, “জলধর একটা কাজের কাজ করেছে। সিবি-ই তোকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে গোরা।”
চারু পাইপের ছাই খোঁচাতে খোঁচাতে বলল, “উদ্ধার করতে পারব কিনা জানি না। চেষ্টা করব। তার আগে কয়েকটা কথা বলে নিই সলিলবাবু। কলকাতায় আজকাল বেশ কয়েকটা প্রাইভেট ইনটেলিজেন্স এজেন্সি হয়েছে। তারা নানা রকম কাজ করে। এমন কি সিকিউরিটি সার্ভিসও। আমরা সবরকম কাজ করি না। আমাদের ফার্ম ছোট। আমরা স্পেশ্যালাইজড কাজ নিই। তবে খুবই যত্ন করে করি।”
“আপনারা কী কী কাজ করেন?” সলিল বলল।
“প্রথমে মেটরিমোনিয়াল কাজকর্ম। ধরুন, পাত্র বা পাত্রী পক্ষ—সিক্রেটলি কিছু ইনফরমেশান চাইল, ফ্যামিলি সম্পর্কে, ছেলেমেয়ে সম্পর্কে। আমরা সেটা যোগাড় করে দি। তারপর হল ডিভোর্সের ব্যাপারে পার্টিকে তাদের দরকার মতন ইনফরমেশান সাপ্লাই করা। “
মানিক বলল, “বাঃ! বিয়ে আবার বিবাহ-বিচ্ছেদ! আপনারা তো মশাই গাছেরও খান, তলারও কুড়োন!”
চারু বলল, “সরি, গাছ দু জাতের। একই গাছের নয়।”
নিয়োগী বলল, “আর কী করেন স্যার?”
“ব্ল্যাকমেলিং কেস। আপনাকে কেউ ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করছে—আপনি আমাদের কাছে এসে ক্লায়েন্ট হলেন। তারপর দেখুন সেই ব্ল্যাকমেইলারকে কী করি!”
সলিল বলল, “গোরার কেসটা ব্ল্যাকমেইল বলে চালানো যাবে?”।
“এখনই বলতে পারছি না। সব শুনতে হবে ভাল করে— তারপর ভেবে দেখব।”
জলধর গোরাচাঁদকে বলল, “গোরা, আমি সবই বলেছি যতটা পারি। এবার তুই বল। নিজের কেস নিজে বলাই ভাল। ”
গোরাচাঁদ বলব-কি বলব না করে তার বিপদের কথা বলতে লাগল।।
গোরাচাঁদের বৃত্তান্ত শেষ হল যখন তখন ঘড়িতে সাড়ে ন’টা। গরমের দিন। সাড়ে নটা এমন কিছু রাত নয়। আচ্ছা ভাঙতে প্রায়ই দশ সোয়া দশ বেজে যায়। কাজেই জলধররা কেউ চঞ্চল হল না।
সিগারেট খুঁজতে খুঁজতে সলিল চারুর দিকে তাকাল। অর্থাৎ বলতে চাইল, শুনলেন তো সব—এবার বলুন কী করা যায়?
চারু কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল। ভাবছিল। চোখ বন্ধ করে আরও কিছুক্ষণ বসে থাকার পর চোখ খুলল। তারপর গোরাচাঁদকে বলল, “আপনি কী করতে চান?”
“আমি! আমি কী চাইব?”
“মানে মেয়েটিকে বিয়ে করতে চান? না, তাকে হটাতে চান?”
ওই মেয়েকে বিয়ে! অসম্ভব! মশাই, ওই মেয়েকে কেউ বিয়ে করে? কালীর খাঁড়া। ডেনজারাস মেয়ে। অসভ্য, ভালগার, পাজি…। না, ওকে আমি বিয়ে করব না। নেভার।”
“বাড়িতে একবার বলে দেখুন না?”
“আমার ঘাড়ে কটা মাথা যে বাড়িতে বলব! আমার জেঠামশাইকে আপনি চেনেন না।জেঠার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার সাধ্য আমার নেই। এমনিতেই বাড়িতে বিয়ের বাজার বসে গেছে। আজ বেনারসি, কাল বালুচরি, পরশু স্যাকরা, তরশু ফার্নিচার…। না মশাই ও কাজ আমার দ্বারা হবে না। তবে হ্যাঁ, দিদি এলে বলতে পারি। দিদি দুর্গাপুর থেকে কবে আসবে তাও জানি না। এদিকে দেখতে দেখতে দিন চলে যাচ্ছে…।”
জলধর বলল, “চারু, বিয়েটা ভেঙে যাওয়াই দরকার। মেয়েটাকে তুই প্যাঁচে ফেলে দে। এমন কিছু একটা কর, যাতে মেয়ে পক্ষের আর মুখ না থাকে কিছু বলার। দু একটা ব্ল্যাক স্পট লাগিয়ে দে। এমনিতেই বিয়ে ভেঙে যাবে।”
গোরাচাঁদ তাড়াতাড়ি বলল, “না না, নোংরা কিছু করবেন না। হাজার হোক ভদ্রবাড়ির মেয়ে। ব্ল্যাক স্পট লাগালে কেচ্ছা হয়ে যাবে। সেটা উচিত নয়।”
মানিক রগড় করে বলল, “উঃ, দাদার যে বড় দরদ। তোমার ক্যারেকটারে যখন স্পট লাগাল। ”
“সবাই সব পারে না। আমি ভদ্রলোক। ইতরামি করতে পারব না।”
চারু বলল, “আসলে আপনি চাইছেন, সাপও মরে, লাঠি না ভাঙে। তাই না?”
“হ্যাঁ।”
“বেশ দেখি কী করতে পারি! তা এ সব করতে হলে কিছু টাকা পয়সা লাগবে। কত তা বলতে পারছি না। হাজার দুই চার হতে পারে।”
গোরাচাঁদ মাথা নেড়ে জানাল, তার আপত্তি নেই।
চার
জ্যৈষ্ঠ মাসের ফাঁড়াটা কাটল। জেঠাইমার দয়ায়। এখন আষাঢ় চলছে। পাঁজিতে আষাঢ় মাসের মাঝামাঝির আগে বিয়ের দিন নেই। প্রথমটা দিনটা পড়েছে বৃহস্পতিবার, দ্বিতীয়টা শনিবারে। বৃহস্পতিবারে জেঠাইমা বিয়ে দেবে না। শনিবারে মেয়ের তরফে আপত্তি। কাজেই সেই একেবারে আষাঢ়ের শেষে সোমবার দিনটাই মোটামুটি ঠিক। আর তা না হলে শ্রাবণের গোড়ায়।
আষাঢ় মাসের দু’ একটি দিন, গোড়ায় গোড়ায়, আকাশ ঘোলাটে, মেঘ হল, বৃষ্টি হল না। তারপর বৃষ্টি নামল। দিন দুই ভাল বৃষ্টি হল। আবার রোদ। রোদ-বৃষ্টির মাঝখানে পড়ে গোরাচাঁদের সর্দি লেগে গেল। বর্ষার সদি। জেঠামশাই অন্য কাজে ব্যস্ত বলে গোরাচাঁদকেই সোদপুরের কারখানা আর শোভাবাজারের অফিস সামলাতে হচ্ছিল। এমন সময় সর্দিজ্বর।
গোরাচাঁদ জ্বর গায়ে সেদিনও বেরুতে পারেনি। জ্বর ততটা নয়, একশো এক ছুঁয়েছে, কিন্তু নাক, গলা, মাথার অবস্থা খারাপ। নাক বুজে আছে, গলায় অসম্ভব ব্যথা। টনসিল ফুলেছে, গলার স্বর ভাঙা। মাথার কথা আর কী বলবে গোরাচাঁদ—ছিঁড়ে যাচ্ছিল যেন। ভীষণ যন্ত্রণা।
সন্ধেবেলায় গোরাচাঁদ খানিকটা গরম নুনজলে গার্গল করে ঘরে আসতেই দেখল, ফুটকি কী একটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
ভাঙা গলায় গোরাচাঁদ বলল, “ওটা কী রে?”
ফুটকি বলল, “পুরনো ঘিয়ে আদার রস, রসুন, মধু দিয়ে মেড়ে কফের ওষুধ। বুকের সর্দি তুলে দেবে। গলা পরিষ্কার হবে।”
নাকমুখ কুঁচকে বমির ভাব করে গোরাচাঁদ বলল, “কে দিল? পুরনো ঘিয়ে আদার রস! তোর কবরেজি?”
ফুটকি বলল, “আমার নয়, জেঠাইমার। জেঠাইমাকে কে বলেছে!”
“ফেলে দে। ভদ্রলোকে ওসব অখাদ্য খায় না। একে পুরনো ঘি তায় আদার রস, তার সঙ্গে মধু। ওদিকে আবার রসুন। কী কম্বিনেশন! ফেলে দে।”
ফুটকি বলল, “ফেলে দিতে হয় তুমি দাও। আমি রেখে যাচ্ছি।”
ফুটকির ভাল নাম লীলা। কাছাকাছি পাড়ার মেয়ে। জেঠাইমার সঙ্গে লীলার মায়ের খুবই বন্ধুত্ব। লীলার বাবা কচিকাচাদের ডাক্তার। একটু খেপাটে। নাম আছে ডাক্তার হিসেবে, পয়সা তেমন নেই।
গোল মতন ছোট বাটিটা রেখে ফুটকি চলে যাচ্ছিল, গোরাচাঁদ বলল, “তুই কি বাড়ি চললি?”
“হ্যাঁ। সাতটা বাজল। বৃষ্টি আসতে পারে।”
“তা যাবার আগে আমাকে কড়া করে এক কাপ চা খাইয়ে যা। আগুনের মতন গরম। গলাটা জ্বলে যাচ্ছে। কেমন বসে আছে দেখছিস না। শব্দ বেরুচ্ছে না। কী রকম শোনাচ্ছে রে আওয়াজটা?”
ফুটকি দু’ পলক দেখল গোরাচাঁদকে। তারপর অক্লেশে বলল, “গাধার মতন। ” বলে চলে গেল।
গোরাচাঁদ থ’ মেরে গেল। ফুটকির কথাবার্তা বরাবরই বেমক্কা। যা মুখে আসে বলে দেয়। কোনও বাদ-বিচার নেই। গোরাচাঁদকে তোয়াক্কা করে না। মান্য তো নয়ই। আসলে মেয়েটা এ-বাড়িতে ছেলেবেলা থেকে আসছে যাচ্ছে বলে ওর কোনো সঙ্কোচ আড়ষ্টতা নেই। কিছুই গ্রাহ্য করে না। আগে তো গোরাচাঁদকে ‘তুই’ বলত। বয়েসে বছর পাঁচেকের ছোট। আজকাল অবশ্য ‘তুমি’ বলে তাও যেন বাধ্য হয়ে। বেশি আস্কারা মেয়ে ও মাথায় উঠেছে। জেঠাইমাই ওকে মাথায় তুলেছে। তবে মেয়েটা ন্যাকা নয়। সাফ-সুফ কথা বলে। এক সময় মেয়েদের ফুটবল খেলত। আঁটসাঁট চেহারা। মাথায় একটু বেঁটে। মেয়েদের স্কুলে ভূগোল পড়ায়। ও আবার জলধরের শালী হয় সম্পর্কে। জলধরের বউয়ের মাসতুতো বোন।
গোরাচাঁদ অবশ্য ‘গাধা’ শব্দটায় খুশি হল না। কিন্তু এখন তার দিন ভাল যাচ্ছে না। যার যা খুশি বলে গেলেও তাকে মুখ বুজে সহ্য করতে হচ্ছে। সেই মশলা-বাড়ির মেয়েটা, মানে গুঁড়ো মশলার কারবারি ফটিক দত্তের মেয়েটা, আজ ক’দিন চুপ মেরে আছে। মাঝে একদিন ছাড়া আর ফোন করেনি। ফোন করে অবশ্য সেদিন বলেছে, সোনার চাঁদ গোরাচাঁদকে সে হাতিবাগানের বাজারের কাছে বাগে পেয়েছিল। ইচ্ছে করলেই গাড়ির জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে চাঁদের মাথায় চাঁটি মারতে পারত। দয়া করে মারেনি।
তারপর আর ফোন আসেনি। গোরাচাঁদ আজকাল ফোনের ডাক পেলেই ভয়ে কুঁকড়ে যায়, গলা দিয়ে শব্দ বেরুতে চায় না! দরদর করে ঘামতে থাকে।
বন্ধুদের ওপরেও গোরাচাঁদ বেশ ক্ষুন্ন হয়ে উঠছিল। ওরা কোনও কর্মের নয়। কিছুই করল না। এতদিনের বন্ধু, এত মাখামাখি, ভাব-ভালবাসা, দায়ে অদায়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা, সেই বন্ধুরাই তাকে একা হাড়িকাঠের সামনে রেখে সরে থাকল। লাভের মধ্যে গোরাচাঁদের হাজার দেড়েক টাকা গচ্চা গেল। ওই চারু বাঁড়ুজ্যেকে দিতে হয়েছে।
কী করেছে চারু? কিস্যু নয়। মেয়ের নাম ধাম ছবি, মেয়ের বাপের খোঁজ-খবর সব নিয়ে দিব্যি বসে আছে। জলধর কোত্থেকে একটা ফালতু, বাজে লোক ধরে আনল। কে জানে লোকটা চিট ক্লাসের কী না?
বড় দুঃখেই গোরাচাঁদ বড় করে নিশ্বাস ফেলতে গেল, নাক বন্ধ থাকার জন্যে পুরোপুরি ফেলতে পারল না, বাতাস আটকে গেল।
এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। কারা যেন আসছে।
প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সলিলরা ঘরে ঢুকল। চার বন্ধু, আর সেই দাড়িঅলা চারু।
“কি রে? তোর নাকি চার পাঁচ জ্বর! হেপাটাইটিস? না, ম্যালেরিয়া?” সলিল বলল।
গোরাচাঁদ বন্ধুদের দেখছিল। বলল, “কে বলল?”
“বাজারে খবর! তা কী হয়েছে তোর? হেভি টাইপের ম্যালেরিয়া?”
“না। কে বলেছে তোদের আমার ম্যালেরিয়া হয়েছে?”
“হলেই হয়। কলকাতা শহরে আকচার ম্যালেরিয়া হচ্ছে।”
“আমার সর্দিজ্বর হয়েছে। কমন কোল্ড। ইনফ্লুয়েঞ্জা!”
“তাই নাকি! তা ভাল। বাঁচালি।
“ নিয়োগী বলল, “তুই বাড়ি থেকে বেরুচ্ছিস না?”
“দু’ দিন বেরোইনি। কারখানা অফিস দু’ দিক দেখতে হচ্ছিল। তার ওপর বৃষ্টি বাদলা। ”।
“কেমন আছিস এখন?”
“জ্বর। গলা বুজে আছে। মাথায় যন্ত্রণা। গা-হাত ভেঙে যাচ্ছে।”
মানিক বলল, “সেরে যাবে দাদা। মেরে কেটে সাত দিন। তবে ক্যালকাটা ফিভার হলে দশ পনেরো দিনের ধাক্কা। শরীরটা বেশ উইক করে দিয়ে যাবে। তা তাতে একদিক থেকে ভাল। আষাঢ় মাসটাও তুমি কাটিয়ে দিতে পারবে। শরীর দুর্বল হলে বিয়ে করা যায় না। এখন আমাদের টাইম দরকার। তুমি যদি আরও একটু বেয়াড়া অসুখ বাধাতে পারতে, শ্রাবণ মাসটাও গড়িয়ে দেওয়া যেত।”
ঠিক এই সময় ফুটকি ঘরে এল। গোরাচাঁদের জন্যে গরম কড়া চা এনেছে।
ফুটকিকে দেখেই জলধর বলল, “কী গো? তুমি! যাক, দেখা হয়ে গেল! কোনো খবরই পাই না। কেমন আছ? খবরটবর ভাল?”
ফুটকি হাসল। “আপনারা ভাল?” বলে সলিলদের দিকেও তাকাল। হাসি হাসি মুখ। সলিলরা সকলেই ফুটকিকে চেনে। এবাড়িতেই দেখছে বরাবর।
একমাত্র চারুই ফুটকিকে চেনে না।
জলধর চারুকে বলল, “চারু, আমার শালী লীলা। অনেক ভাগ্যে এমন শালী পেয়েছি। লীলা খেলোয়াড়। লেডিজ ফুটবলে স্ট্রাইকার পজিশনে খেলত।”
চারু চকচকে চোখ করে হাসল। বলল, “বাঃ। আমি এই প্রথম মেয়ে ফুটবলার দেখলাম। এখনও খেলেন?”
জলধর বলল, “না, এখন আর—কই—খেলাটেলা…। তা তোমার হাতে ওটা কী?”
“চা। গোরাদার জন্যে!”
“আমাদের জন্যেও একটু হয়ে যাক ভাই। গোরাকে চা না খাইয়ে অন্য কিছু খাওয়ালে পারতে। এনার্জি পেত। চায়ে মুখ আরও বিস্বাদ হয়ে যাবে। ইনফ্লুয়েঞ্জায় বেশি চা খেতে ভাল লাগে না।”
মানিক বলল, “দাদার চেহারা দু দিনেই যা হয়েছে। মনে হচ্ছে সলিড টায়ার পাঞ্চার হয়ে গিয়েছে।”
ফুটকি বলল, “আকুপাঞ্চার।”
হেসে উঠল সকলেই একসঙ্গে। অট্টহাসি।
গোরাচাঁদ অপ্রতিভ। সে হাসতে পারল না। ফুটকির ওপর চটে গেল। বন্ধুদের সামনে এই রসিকতার কী মানে হয়! ঠিক আছে, এক মাঘে শীত পালায় না। গোরাচাঁদও পরে দেখে নেবে ফুটকিকে।
চা দিয়ে ফুটকি চলে যাচ্ছি।
জলধর বলল, “চায়ের সঙ্গে ঝালটাল কিছু হবে? বড়া ক্লাসের। বর্ষার দিন।”
“জেঠাইমাকে বলছি।”
“থ্যাংক ইউ! তা শ্যালিকা, খবরটবর বললে না?”
“ভালই। ”
জলধর আর ফুটকির মধ্যে খুব সাবধানে, আড়ালে চোখাচুখি হল। ফুটকি চলে গেল। জলধর চারুর দিকে তাকিয়ে কেমন করে যেন চোখ টিপল। ছোট করে। বলল, “নিজের শালী বলে বলছি না, চারু। লীলা ভালই খেলত। আমি দেখেছি ওর খেলা। বুদ্ধি করে খেলতে পারত। বেশ মেয়ে।”
গোরাচাঁদ অন্যমনস্কভাবে চায়ে চুমুক দিল। দিয়েই ‘উঃ’ করে উঠল। চা যে এত আগুন গরম বুঝতে পারেনি। জিভ পুড়ে গেল।
সলিল বলল, “কী হল রে? জিভ বার করে বসে থাকলি?”
গোরাচাঁদ জিভ সামলাতে সামলাতে বলল, “ভীষণ গরম। জিভ ঠোঁট পুড়ে গেল।
মানিক মজা করে বলল, “একটু দেখেশুনে খাও, দাদা! চোখ চেয়ে দেখো।”
সলিল ততক্ষণে আরাম করে বসে পড়েছে। সিগারেট ধরাচ্ছিল। বলল, “তোর কিছু ভাল খবর আছে, গোরা। গুড নিউজ। চারুবাবু অনেকটা সাকসেসফুল। ”
গোরাচাঁদ প্রত্যাশাই করেনি চারুর কাছ থেকে কোনো ভাল খবর শুনতে পাবে। কথাটা কানে যাওয়া মাত্র সে চারুর দিকে তাকাল। চোখে কৌতুহল।
চারু বলল, “কাজ অনেকটাই এগিয়েছে গোরাবাবু। আমি মাঝে আর কোনো খবর .দিতে পারিনি আপনাদের। তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি। কাজটাই তো আসল। ইন ফ্যাক্ট আমি আপনার ব্যাপার নিয়ে ভীষণ বিজি ছিলাম। কম কাঠখড় পোড়াতে, ঘোরাঘুরি করতে হয়নি।”
জলধর চারুকে বলল, “কতটা এগিয়েছ, তাই বলো গোরাকে।”
গোরাচাঁদ মাথা হেলাল। অর্থাৎ সে জানতে চায় কাজের কাজ কী হয়েছে?
চারু বলল, “প্রথমত আমি আপনাকে মেয়েটির বাড়ির ব্যাপারে অনেক কথাই বলতে পারি। ফ্যামিলি ইনফরমেশান। তারপর ওদের বিজনেস সম্পর্কেও খোঁজ-খবর করেছি। ভালই চালাচ্ছে। মাসে হাজার পঞ্চাশ টাকার বিজনেস করত। এখন ঢিলে যাচ্ছে কিছুদিন। প্রোডাক্ট খারাপ হয়ে গিয়েছে হালে। দেদার ভেজাল দিচ্ছিল। ওদিকে…”
বাধা দিল গোরাচাঁদ। মেয়ের বাপের ব্যবসা সম্পর্কে জানার কোনো আগ্রহ তার নেই। বলল, “বাপ বাদ দিন, মেয়ের কথা বলুন।”
চারু বলল, “মেয়ে, কী বলব, এমনিতে খারাপ নয়। দেখতে-শুনতে ভাল। লেখাপড়াও করেছে খানিকটা। তবে মেয়েটি একটু রোগা আর লম্বা। একটা চোখ সামান্য টেরা। তা এসব ঠিক আছে। স্বভাবটাই ঠিক নেই। রুক্ষ টাইপের, বদমেজাজি, ঝগড়ুটে। তা ছাড়া ওর একটা মেন্টাল—মানে সাইকোলজিক্যাল সিকনেস—গোলমাল আছে। ইনসমনিয়ায় ভোগে, রাত্তিরে যেখানে সেখানে ফোন করে, চেনা অচেনা মানে না, যা মুখে আসে বলে…!”
“পাগল?” গোরাচাঁদ বলল, প্রায় আঁতকে উঠে।
“না, পাগল ঠিক নয়, ওই ছিট টাইপের। তা তার চেয়েও বড় কথা ওর একজন—আই মিন—ওই কমলিকা মেয়েটির একজন ফ্রেন্ড আছে। লাভার। তা চার পাঁচ বছর ধরে দু’জনের লাভ চলছে। লুকিয়ে ঘোরাফেরা, খাওয়া-দাওয়া। চিঠিচাপাটিও চলে। এরকম একটা চিঠি আমি হাতাতে পেরেছি। মেয়েটির লেখা।”
গোরাচাঁদ বলল, “লাভার! প্রেম! ও তা হলে এই বিয়েতে…”
“একেবারেই রাজি নয়, একদম নয়। ওর বাড়ি থেকে জোর করে এই বিয়েটা চাপাচ্ছিল। মেয়ে বলেছে, এই বিয়ে ঠিক হলে ও হয় বাড়ি থেকে পালাবে, না হয় গলায় দড়ি দেবে। বাড়ির লোক এখন খানিকটা ঘাবড়ে গেছে। তবে পিছিয়ে যায়নি।”
গোরাচাঁদ বলল, “ভীষণ অন্যায় কথা। বাড়ির লোক এভাবে জোর করতে পারে না।”
মানিক বলল, “দাদা, ওর বাড়ির লোক নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। মেয়েকে নিয়ে মাথা ঘামাও। প্রেম করা খেপি মেয়েকে তুমি কিছুতেই বিয়ে করতে পারো না!”
“আমি কি করব বলেছি! আশ্চর্য!”
“তা হলে তুমি এবার বেঁকে দাঁড়াও। তোমার রিজেকশান স্লিপ পাঠিয়ে দাও।”
“কাকে?”
সলিল কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই নিয়োগী বলল, “গোরা, দিস ইজ দি মোমেন্ট। গোল্ডেন অপারচুনিটি। কথাটা তুই জেঠাইমাকে বলে দে।”
গোরাচাঁদ ভেতরে ভেতরে খুশি হচ্ছিল। প্রেম-করা খেপি মেয়েকে তো তার গলায় ঝোলানো যাবে না। জেঠামশাই জানতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে খারিজ। ক্যানসেল। বলল, “জেঠাইমাকে বলা কি ঠিক হবে! ওদের ভেতরের কথাবার্তা। তার চেয়ে দিদিকে বলাই ভাল। দিদিকে বলতে পারি।”
“তাই বল।”
“কিন্তু প্রমাণ। দিদি যখন বলবে, কিসের উড়ো খবর শুনে এইসব বাজে কথা বলছিস? ভদ্দরলোকের বাড়ির মেয়ের নামে মিথ্যে গুজব রটানো ভাল নয়। নোংরামির কাজ। বাবা যখন জানতে চাইবে, প্রমাণ কী? তখন? কী বলব বাবাকে?… দিদি তো ভাই ছেলেমানুষ নয়, জামাইবাবুও পাকা লোক।”
“প্রমাণ?” সলিল বলল, “প্রমাণ পেলেই তুই এগিয়ে যাবি! এই তো?”
“হ্যাঁ।”
“ঠিক আছে। প্রমাণ চারুবাবুর কাছে আছে।”
চারু বলল, “আমি আপনাকে প্রমাণ দিয়ে যাচ্ছি। শুধু চিঠি নয়, একটা ফটোও। যাতে ফটোর পেছনে কমলিকা লিখেছে, রাজুকে আমার ভালবাসার সঙ্গে।”
“টু রাজু, উইথ মাই লাভ!” মানিক রগড় করে বলল।
“রাজু কে?”
“ওর লাভার।”
“কই চিঠি? ফোটো কোথায়?”
চারু বলল, “দিচ্ছি। তার আগে আর-একটা কথা বলে নিই গোরাবাবু! মেয়েটি হয়তো আপনাকে আবার একদিন ফোন করবে। দু’ চারদিনের মধ্যেই। সারেন্ডার করতে পারে, কিংবা দু’ দশটা রাফ কথা বলতেও পারে। আপনি তখন সমানে সমানে লড়ে যেতে পারেন। ওকে নক আউট করতে পারেন। তাই না?”
জলধর এতক্ষণ চুপ করে ছিল। এবার বলল, “গোরা, হাতে ব্রহ্মাস্ত্র পেয়েও যদি তুই বেটা বখরি হয়ে থাকিস—ধিক তোকে। ধিক আমাদের।”
গোরাচাঁদ উত্তেজিত হয়ে বলল, “করুক ফোন, আমি ওকে দেখে নেব।”
পাঁচ
যে ফোনের নামে এতদিন গোরাচাঁদের হৃৎকম্প হত, গলা শুকিয়ে যেত ভয়ে—সেই ফোনের প্রত্যাশায় এখন সে উন্মুখ হয়ে বসে থাকে। অধৈর্য হয়ে ওঠে। দিন চারেক কেটে গেল। কোনো ফোন নেই। ছ’ দিনের মাথায় ফোন এল। রাত প্রায় ন’টা নাগাদ। বাইরে তখন তুমুল বৃষ্টি নেমেছে। বারান্দায় গিয়ে গোরাচাঁদ ফোন ধরল। উত্তেজনায় হাত কাঁপছে। ও দিকে প্রবল বৃষ্টি, মেঘগর্জন, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আর এই সময় সব অন্ধকার হয়ে গেল হঠাৎ। লোডশেডিং।
ফোন তুলতেই সেই গলা, তবে আজ একটু চাপা, ধীর, সামান্য জড়ানো। “কে, সোনার চাঁদ নাকি?”
গোরাচাঁদ কোনো জবাব দিল না।
“কী গো, গোরাচাঁদ শুনতে পাচ্ছ না। কালা হয়ে গেলে?”
“শুনছি।”
“বাঃ, এই তো! কথা ফুটেছে। ” বলেই হাসি।
গোরাচাঁদ নিজেকে সামলে নিয়েছে ততক্ষণে। কড়া গলায় বলল, “শুনুন, আপনি হাসি থামান। এতদিন তো একতরফা খুব হেসেছেন। রসিকতা করেছেন। অপমান করেছেন আমাকে। এবার যে আপনাকে কাঁদতে হবে।”
“কাঁদতে হবে! কেন মশাই! কী দুঃখে!… খুব বৃষ্টি হচ্ছে। একটু গলা তুলে কথা বলো গোরাচাঁদ। তোমার গলা ভাল শুনতে পাচ্ছি না! বাব্বা, কী জোর বাজ পড়ল।”
গোরাচাঁদ বাঁকা গলায় বলল, “আসল বাজটা তো পড়েনি। পড়বে।”
“তাই নাকি? কোথথেকে?”
“আমার কাছ থেকেই।… শুনুন—শুনতে পাচ্ছেন—রাজুকে চেনেন। রাজু! মনে পড়ছে!”
“রাজু। মনে পড়বে না কেন! রাজু আমার বন্ধু।”
“শুধু বন্ধু? না, আরও বেশি। লাভার।”
“লাভারই তো! অনেক দিনের।”
“তা তো দেখতেই পাচ্ছি। বড় বড় চিঠি লেখা হত। আমার আদরের, রাজু। তাই না। একটা চিঠি এনে পড়ব?”
“পড়তে পারো। আমার কাঁচকলা হবে। প্রেম করি, চিঠি লিখি। বেশ করি। তাতে তোমার কী গো নদের চাঁদ!”
গোরাচাঁদ ঘাবড়ে গেল। কী মেয়ে রে বাবা! একটুও দমল না, ভয় পেল না। কী বলবে বুঝতে না পেরে সে বলল, “ওদিকে প্রেম হচ্ছে, আর এদিকে—”
“মশাই, প্রেম নয় শুধু চুটিয়ে প্রেম। রাজু কি স্মার্ট, কী রকম ম্যানলি দেখতে, হ্যান্ডসাম! তোমার মতন গোবরগণেশ, হাঁদা, রসগোল্লা নাকি সে?”
গোরাচাঁদ চটে গেল। পড়ক বৃষ্টি। চেঁচিয়ে বলল, “শাট আপ। কথা বলতে শেখেননি? অসভ্য, অভদ্র, থার্ড ক্লাস! ন্যাস্টি! লজ্জা করে না, একটা ছেলের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করেন বলছেন—আর এদিকে বিয়ের—”
“কে তোমাকে বিয়ে করতে কেঁদে মরছে নদের চাঁদ! আমি তো গোড়া থেকেই বলছি—লেজ গুটিয়ে পালাও। নয়ত বিপদে পড়বে।”
“চুপ করুন। আমি বিয়ে করছি না। আপনার মতন অসভ্য ন্যাস্টি মেয়েকে কোনো ভদ্রলোক বিয়ে করে না। এ বিয়ে হবে না। আমি ব্যবস্থা করছি।”
“আঃ! বাঁচা গেল!”
“হ্যাঁ, বাঁচা গেল। আমি বাঁচলাম।”
হঠাৎ কী যে হল, ফোনের ওপারে হাসির লহরা ছুটল। কী জোর হাসি। হাসতে হাসতে যেন মরে যাবে মেয়েটা। হাসছে তো হাসছেই। জোরে, ধীরে, লহর তুলে, ছররার মতন হাসির ধ্বনি ছিটিয়ে হেসেই যাচ্ছে। হাসতে হাসতে ক্রমশ যেন কী একটা হচ্ছিল। স্বর পালটে যাচ্ছিল। গলা অন্যরকম হয়ে আসছিল।
গোরাচাঁদের কানের দোষ। বিরক্ত হয়ে ফোন রেখে দিতে যাচ্ছিল, এমন সময় হাসির দাপট কমল। ভোল্টেজ কমে গেলে আলো যেমন নিভু-নিভু হয়ে আসে, সেইভাবে হাসির দমকা কমে এল। তারপর ওপার থেকে কে যেন বলল, “কী গো?”
গোরাচাঁদ চমকে উঠল। যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। ধরতে পারল গলার স্বর।
“কী গো?”
“ফুটকি!”
“আমি।”
“তুই ওখানে কী করছিস?”
“আমি ওখানে কেন! আমি তো এখানে জামাইবাবুর বাড়িতে।”
“জামাইবাবু! জলধরের বাড়িতে?”
“হ্যাঁ, জলধরদার বাড়িতে আজ আমার নেমন্তন্ন ছিল। যা বৃষ্টি! আর বাড়ি ফেরা হবে না। এখানেই থেকে যাব।”
গোরাচাঁদ বিরক্ত হয়ে বলল, “তুই-তুই এতক্ষণ আমার সঙ্গে রগড় করছিলি। আশ্চর্য!”
“এতক্ষণ কেন করব, বরাবর করছি, এতদিন।”
গোরাচাঁদ যেন আকাশ থেকে পড়ল। ফুটকি, ফুটকি এতদিন তার সঙ্গে মজা করছিল। তাকে বোকা বানিয়ে ছেড়েছে। “ফুটকি তুই—তুই…।”
“তুই তুই কী করছিস?” এবার জলধরের গলা, মানে ফুটকির হাত থেকে ফোনটা সে নিয়ে নিয়েছে। “কুঁতিয়ে কথা বলছিস কেন! স্ট্রেট বল.।”
“জলধর।”
“জলধর মিত্তির। লীলার জামাইবাবু। প্রাণের আরাম। তোরও বন্ধু। …তা কেমন খেলালাম তোকে।”
“শালা!”
“বল, বল। যা খুশি বল।… তা তুই কিছু বুঝলি? তোর যা মাথা, ইট মারলে ইষ্টক হয়ে যায়। তুই মাইরি সত্যি স্টকে এক পিস মালই। বুঝলি কিছু?”
“কী বুঝব?”
“লীলা।”
গোরাচাঁদ সামান্য চুপ করে থাকল। তারপর বলল, “বুঝেছি। তবে ওকে। একেবারে ইয়ে অবস্থা থেকে দেখছি।”
“ভালই তো! ইয়েরাই পরে টিয়ে হয়। আরে তুই নিজের বাগানের গাছের ফল খাবি—তার স্বাদই আলাদা। আমরা তো টুকরির মাল খেয়েছি। ” ও পাশে গুঞ্জন উঠল যেন।
গোরাচাঁদ এবার হেসে ফেলল জোরে। বলল, “তা না হয় খাব। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে কে? ইউ নো মাই জেঠামশাই!”
“কি ভাবিস না তুই। ঘণ্টা আমরা বাঁধব। দিদি বাঁধবে। নিয়োগীকে দিদির কাছে দুর্গাপুরে পাঠানো হয়েছিল। এভরিথিং ও-কে।”
“ও! মানে তোরা সবাই তা হলে…”
“বিন্দুমাত্র সন্দেহ রাখিস না গোরা, সবাই মিলে মাথা খাটিয়েছি। তুই আমাদের বন্ধু, তোর ভাল-মন্দ আমরা না দেখলে কে দেখবে!” জলধর হাসছিল।
শালা! ভাল-মন্দ দেখনেওয়ালা।… তা ওর কী হবে? মশলাবাড়ির মেয়েটার? ভদ্রবাড়ির একটা মেয়েকে নিয়ে তোরা যা কেচ্ছা করলি… ছি ছি!”
জলধর বলল, “তুই ভাবিস না। চারুর এনট্রি পাকা হয়ে গেল।”
চারু! কেন রাজু?”
“ওই একই হল। যা চারু তাই রাজু। টাকার এপিঠ ওপিঠ।”
“কী বলছিস তুই?”
“ঠিকই বলছি। চারু আসলে ফুড ডিপার্টমেন্টে আছে, নলিনীর সঙ্গে। অফিসার। তোর গুঁড়ো মশলার যাওয়া-আসা আছে চারুর কাছে। ইয়ের ব্যাপার থাকে তো—! চারু মশলাবাড়ির সদর পেরিয়েছিল, এবার অন্দরে ঢুকে যাবে। ও নিয়ে তুই ভাবিস না। তোর টাকাও আমার কাছে।”
গোরাচাঁদ ভীষণ অবাক হয়ে বলল, “এখানেও ধাপ্পা! তোরা আমায় বুদ্ধ বানিয়ে ছাড়লি।”
জলধর হো হো করে হাসছিল। বলল, “গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—!”
“থাম, গীতা আওড়াতে হবে না। …ফুটকি আছে? ওকে একবার দে।”
ফুটকি ফোন নিল। “কী বলছ?”
“বলছি, তোর কেরামতি দেখলাম। তা তুই গলাটা পালটাতিস কেমন করে?”
ফুটকি হাসছিল, বলল, “কায়দা আছে। ফোনের মুখে পাতলা রাংতা রাখতাম। একটু পেঁজা তুলো। তা ছাড়া তোমার তো বাঁ কানটা ভাল না।”
“বাঃ! চমৎকার! যেমন জামাইবাবু তেমনি তার শালী।… তা তুই এত কাণ্ড করতে গেলি কেন? ব্যাপারটা কান ঘুরিয়ে নাক দেখানোর মতন হয়ে গেল। সরাসরি দেখালেই পারতিস!”
“যাঃ! নিজে দেখতে জানে না, আবার আমায় বলে!” বলতে বলতে ফোন রেখে দিল ফুটকি।
গোরাচাঁদ ফোন নামিয়ে রাখল। দাঁড়িয়ে থাকল সামান্য। তখনও বৃষ্টি পড়ে চলেছে। গোরাচাঁদের মজা লাগছিল। ভালও লাগছিল। বেশ ঝরঝরে মনে হচ্ছিল নিজেকে। বুকের কাছে কী যেন একটা ঝুলত এতদিন। এখন একেবারে হালকা।
চার তাস
নলিন ফোনে কান রেখে সাড়ার জন্যে অপেক্ষা করছিল; ওপারে গলার স্বর উঠতেই নলিন বলল, “কী ব্যাপার?”
“কিসের কী ব্যাপার!”
“ন’টা পাঁচ থেকে ন’টা তেরো⋯চারবার ফোন তুলেছি⋯এতক্ষণ কার সঙ্গে কথা হচ্ছিল?”
“দিদি কথা বলছিল…”
“দাদার সঙ্গে নিশ্চয়।”
“হ্যাঁ।”
নলিন দু-মুহূর্ত চুপ; তারপর বলল, “তোমার দাদাটি ভেবেছেন কী? বাড়ির ফোন কী তাঁর আর তাঁর গিন্নির মৌরসিপাট্টা?⋯আলাদা ফোন নিতে বলো। বউয়ের ঘরে থাকবে।”
ওপারে চাপা হাসি।
নলিন বলল, “হাসছ যে?”
“দাদাকে বললে দাদা কী জবাব দেবে যদি জানতে…” ওপার থেমে গিয়ে হাসতে লাগল।
“যদি জানতে…” নলিন বলার ভঙ্গি অনুকরণ করে ভেঙাল। “লহর তুলে হাসছ যে! এ্যাঁ⋯! জানার কি আছে শুনতে পাই?”
ওপারের হাসি থামল না, স্টেশনের কাছে গাড়ি পৌঁছে গেলে গতি এবং শব্দটা যেমন মন্থর ও মৃদু হয়ে আসতে থাকে, সেই রকম হাসিটাও ঈষৎ কমে আসতে লাগল। তারই ফাঁকে ফাঁকে কথা। ওপার বলল, “দাদা বলবে, তুমিই আলাদা একটা ফোন তোমার বউয়ের ঘরে রাখো। বাড়ির ফোন তোমারও মৌরসিপাট্টা নয়।”
নলিন থমকে গেল যেন। তারপরই বলল, “মানে—?”
“খুবই সহজ।”
“এ রকম কথা বলার কোনো রাইট পুলিনের নেই। আমি দিনে ক’বার বাড়িতে আমার বউয়ের সঙ্গে ফোনে গল্প করছি। সে হরদম করছে। যখনই ফোন তুলি—দেখি লাইন নেই। তারই উচিত তার বউয়ের ঘরে একটা প্রাইভেট লাইন নেওয়া।”
“তা তুমিই বা হরদম ফোন তোলো কেন?”
“তুলি না।”
“না তুললে কেমন করে জানলে দাদা দিদিতে গল্প হচ্ছে⋯”
নলিন এবার একটু যেন থতমত খেয়ে গেল, সামলে নিল অবশ্য, বলল, “বোঝাই যায়। দেখতেই তো পাচ্ছি। বেলা আটটা সোয়া আটটায় চেম্বারে এসেছে, একটাও পেশেন্ট নেই, টেবিলে পা তুলে বউয়ের সঙ্গে গল্প করছে।”
“পেশেন্ট নেই কেন?”
“থাকলে কেউ সাত সকালে পেশেন্ট ফেলে বউয়ের সঙ্গে গল্প করে?”
“ও!⋯তোমারও বুঝি পেশেন্ট নেই?”
নলিন একেবারে বোবা। মাথা ফেরাতেই চোখে পড়ল তার ডেন্টিস্টস চেয়ারটা শূন্য। জানলা দিয়ে একমাত্র যা রোদই ঘরে এ-যাবৎ এসেছে, এসে দিব্যি সেই চেয়ারে বসে আছে। নলিন হেসে ফেলল। তারপর গলার সুর পাল্টে ডাকল, “ফুলটুসি!”
“শুনেছি, বলো—”
“আমার ঘরে একজন পেশেন্ট আছে।”
ওপারে বুঝি বিস্ময় এবং সামান্য বিব্রত হবার শব্দ এল।
নলিন বলল, “পেশেন্ট বেশ শান্তশিষ্ট, কিন্তু তার দাঁত নেই।”
ওপার অস্পষ্ট করে বলল, “বুড়ো?”
“এখনও হয়নি, হতে হতে দুপুর ফুরোবে।”
“ইয়ার্কি মারা হচ্ছে, না?⋯তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আড্ডা মারার সময় আমার এখন নেই। অনেক কাজ। কী জন্যে ডাকছিলে বলো?”
“কী করছ?”
“স্নান করতে যাব, স্নান করে মার সঙ্গে…”
“সর্বনাশ, এই শীতে এখন স্নান! তোমার না চোখ ফুলে ব্যথা হয়েছে। পুলিন সকালে কী বলল?”
“বলল, কিছু না।”
“কিছু না?”
“না।”
নলিন দু-মুহূর্ত ভাবল, তারপর বলল, “তোমার দিদিকে বলো, আমার বউয়ের চোখ নিয়ে যদি পুলিন ছেলেখেলা করে, তবে আমি তার বউয়ের দাঁত নিয়ে অ্যায়সা হেলাফেলা করব⋯”
ওপার আবার যেন জোরে হেসে উঠল। সেই হাসির মধ্যে কি হল নলিন দেখতে পেল না। দেখতে না পেয়ে জোরে জোরে বলল, “অত হাসির কিছু নেই, আমি পুলিনের বউয়ের ভাঙা দাঁতটা সেপটিক করিয়ে দেব। টিট ফর ট্যাট…”
“তাই নাকি! দিয়েই দেখ, কত মুরোদ বুঝব?”
নলিন প্রায় চমকে গেল। এ যে অন্য গলা, ফুলটুসির নয়, তার দিদির; পাশেই ছিল নিশ্চয়। সঙ্গে সঙ্গে নলিন গলার স্বর পাল্টে নিল। “আরে তুমি! যমুনাপুলিনে⋯। তা, সারা রাত কর কী, সকালবেলাতেও গল্প থামে না। ডিসগ্রেস্⋯! রাম, রাম। চেম্বারে এসে সাত-সকালে কর্তা ফোন করছে আর গিন্নি ফোন ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে চেম্বারে পেশেন্ট বসে। ⋯মিত্তিরবংশে এরকম একটা স্ত্রৈণ আর জন্মায়নি। একেবারে ভেড়ুয়া⋯”
“কে?”
“কে আবার, তোমার হাজবেণ্ড গো, শ্রীমৎ স্বামী…!”
“তাই নাকি! লোকে তো বলে আমার দেওর—।”
“আজ্ঞে না মেমসাহেব, দেওর অন্য জিনিস।”
“জানি তাঁর আবার পুজোয় মন নেই, নৈবিদ্যিতেই চোখ…”
নলিন বুঝতে পারল না, থেমে গেল। অথচ কানে শুনছিল খুব একটা রগড়দার হাসি হচ্ছে ওপাশে, দু-বোনেই হাসছে। নলিন অপ্রস্তুত হয়ে সামান্য চুপ করে থেকে শেষে বলল, “মানেটা বুঝলাম না।”
“বুঝে নাও।”
“মেয়েলি ছড়া মানেই অসভ্য কিছু।”
“ওরে, কি আমার সভ্য পুরুষ।”
“আমি বুঝতে পারছি, তোমার পাল্লায় পড়েই পুলিনটা অসভ্য হয়ে গেছে।”
“তাও ভাল; তা ও না হয় অসভ্যই হয়েছে, আর তুমি যে এদিকে কীর্তি করে রেখেছ। কি মশাই, আমার বোনটার সভ্যসমাজে বের হবার পথ এত তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দিলে⋯।”
ওপাশে কেমন একটা ‘এই’ ‘যা’ ‘মাগো ‘অসভ্য’ ইত্যাদি ভাঙা, বেখাপ্পা, অনুচ্চ-স্বর কথাবার্তা, সলজ্জ হাসি শোনা গেল এবং বোঝা গেল মুখ চাপা দেবার চেষ্টা হচ্ছে। নলিন পরমুহূর্তেই সব বুঝতে পারল। ঈষৎ শিহরিত ও লজ্জিত হয়ে নিতান্ত ভাল ছেলের মতন নলিন আমতা আমতা করে বলল, “তুমি একেবারে ভল্গার। যাক গে, দয়া করে কথাটা গেজেট করে দিও না। যা পেট পাতলা মানুষ। ⋯বুঝলে⋯ ! প্লিজ। কৃতজ্ঞতার একটা পুরস্কার আছে, আমি তোমার আর পুলিনের জন্যে কম করিনি।”
“বড় ভাইকে পুলিন কি? দাদা বলো।”
“দরকারে মানুষ বাবা বলে। যাক সে পরে হবে!⋯তুমি কিন্তু এখন কোনো কিছু ফাঁস করবে না। মাইণ্ড দ্যাট। ⋯আমার হাতেও অস্ত্র আছে।” নলিন হেসে ফেলল।
দুই
এরা এই রকমই, পুলিন, নলিন এবং তাদের বউ। লোকে বলে, তাসের প্যাকেট। অর্থাৎ তারা বোঝাতে চায়, তাসের যেমন চার বাহার, দুই কালো দুই লাল, নয়ত তাসই হয় না, এরাও তেমনি, কাউকে বাদ দেবার উপায় নেই।
পুলিন এবং নলিনের একটা চলতি নাম আছে এ শহরে বাঙালিদের মধ্যে। পুলিনকে বলা হয় ‘চক্ষু’, আর নলিনকে ‘দন্ত’; পুলিন চোখের ডাক্তার বলেই তাকে ঠাট্টা করে যে ‘চক্ষু’ বলা হয় একথা পুলিনও জানে; আর নলিনও জানে সে দাঁতের ডাক্তার বলে তাকে ‘দন্ত’ বলা হয়। এ ব্যাপারে তাদের বিন্দুমাত্র রাগ নেই। রাগ করে লাভ কি, যারা বলে তারা হয় ঠাট্টা করে বলে, না হয় আদর করে তামাশা করে। ওদের মধ্যে কেউ হয়ত পুলিন নলিনের আবাল্য বন্ধু, কেউ হয়ত তাদের বাবার বন্ধু, রীতিমত গুরুজন ব্যক্তি, যাঁদের কাউকে পুলিনরা হয়ত বলে জ্যেঠামশাই, কাউকে কাকাবাবু। অবশ্য এই ঠাট্টার ডাকটুকু সর্বদার নয়, সকলের কাছেও নয়। মুখোমুখি দেখা হলে, ‘পুলিন, নলিন’ কদাচিৎ কোনো বন্ধু হয়ত বলল, ‘এই যে চক্ষু দন্ত, যাচ্ছিস কোথায়?’
পুলিনরা এ শহরে তিন-পুরুষ বসবাস করছে। ঠাকুরদা ছিলেন সিভিল সার্জন, বিহারের যত রাজ্য ঘুরে রিটায়ার করার পর জলবাতাস, গঙ্গা এবং গাছপালা পাহাড়ের জন্যে এখানে এসে স্থায়ীভাবে বসলেন। বাড়িঘর তৈরি হল, ঠাকুরদাদা মারা গেলেন। বাবা অন্য কোথাও গেলেন না, এই শহরের আদালতেই ওকালতি শুরু করলেন, এবং দেখতে দেখতে প্রতিষ্ঠা পেলেন।
ক্ষিতীশ মিত্তির (পুরো নাম ক্ষিতীশচন্দ্র মিত্র) এ শহরে একটা মানুষের মতন মানুষ ছিলেন। বেহারিদের ধারণা ছিল, মিত্তিরবাবুর মতন উকিল পাটনাতেও নেই, আর ‘লালচ্’ থাকলে উকিলবাবু পাটনায় গিয়ে লাখো টাকা কামাতেন। ‘সাচ্চা আদমি’ ছিলেন উকিলবাবু। বাঙালিরা বলত, দেবতুল্য ব্যক্তি। শ্রদ্ধাভক্তি করত, ভালবাসত, বিপদে-আপদে শরণাপন্ন হত, অভিভাবকের মতামতের মতন তাঁর মতামত মান্য করত।
মানুষটি ছিলেন নিরহঙ্কার, কর্মী, আমুদে; এমন কি থিয়েটারপাগলও। ওকালতিতে তাঁর পশার ছিল হিংসে করার মতন, তবু তিনি জীবনটা নথিপত্র আদালত করে শেষ করে দিতে চাননি। দুর্গাবাড়ির পাকা ঘর, কালীবাড়ির গায়ে লাগানো লাইব্রেরি এবং স্টেজ ইত্যাদি ক্ষিতীশ মিত্তিরই করেছিলেন। এই শহরের মধ্যে কলেজ করার পেছনেও তাঁর পরিশ্রম ছিল।
এমন একজন মানুষ মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়সে মারা গেলেন ভাবতেই কেমন লাগে যেন। শিবরাত্রির দিন যে মানুষ সারা রাত ‘কর্ণার্জুনে’ কর্ণের পার্ট করেছেন, সেই মানুষ পরের দিন জ্বরে পড়লেন, জ্বর হু-হু করে বাড়ল, চারদিনের দিন ডবল নিওমোনিয়ায় মারা গেলেন। বাঙালি মহল্লার লোক ক্ষিতীশ মিত্তিরের বাড়ি ঘিরে তিনদিন সমানে বসে ছিল, যেন যমকে কোন পথ দিয়েই ঢুকতে দেবে না। ছোটাছুটি, ডাক্তার ডাকাডাকি, এটা-সেটা করতে বেহারিরাও পিছপা হয়নি, মনিরামের গাড়ি গিয়েছিল পাটনার সবচেয়ে বড় ডাক্তার নিয়ে আসতে, ডাক্তার আসার আগেই ক্ষিতীশ চোখ বুজে ফেললেন চিরকালের মতন।
শোকটা সকলেরই গায়ে লেগেছিল। পুলিন তখন সবে কলেজে ঢুকেছে, নলিন স্কুলে। অভিভাবক বলতে শুধু তাদের মা। দিদি জামাইবাবু তো দূরে থাকে। অবশ্য পাড়ার লোক সবসময়ই কাছে ছিল। শোকের পর্বটা আস্তে আস্তে কাটল। প্রভাময়ী নিজেকে সামলে নিলেন।
আই-এস-সি পাশ করে পুলিন চলে গেল পাটনা মেডিকেল কলেজে পড়তে। ক্ষিতীশবাবুর সেই রকম ইচ্ছে ছিল। তাঁর বাবা ছিলেন সিভিল সার্জন। ইচ্ছে ছিল ছেলে ডাক্তারি পড়ে। ক্ষিতীশের ডাক্তারিটা তেমন পছন্দ ছিল না, তবে বাবাকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, ‘তোমার নাতি পড়বে।’
পুলিন পাটনা থেকে পাশ করে গেল বিলেত, চোখের বিদ্যেতে একটা ডিপ্লোমা আনার জন্যে। সেখানে থাকতে থাকতে ছোট ভাইকে নিয়ে গেল। নলিন শিখল দন্ত চিকিৎসা। পুলিন ফিল আগে, নলিন ফিরল মাস দুই তিন পরে।
পুলিন নলিন অতঃপর এখানেই বসেছে। বাবা চাইতেন না—অর্থ এবং প্রতিষ্ঠার জন্যে ছেলেদের কেউ এই শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যায়। ‘যা করার এখানে থেকেই করবে ; এদের জন্যে করবে।’ প্রভাময়ীরও সেই রকম ইচ্ছে ছিল। শ্বশুরমশাই অনেকটা জমিজায়গা কিনে বাড়ি করেছিলেন, বাগান করেছিলেন; স্বামীর হাতে সেই বাড়ি-বাগান জমি-জায়গা আরও তকতকে হয়েছিল, ছোটখাটো অদল-বদল হয়েছিল। দীর্ঘকাল থাকতে থাকতে এই বাড়ি আর এই জায়গার ওপর যে মায়া জন্মেছিল, সেটা পুরুষানুক্রমে মমতা এবং দুর্বলতা। শ্বশুর ও স্বামী যে ভিটেতে বসবাস করেছেন, শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন, তা ত্যাগ করে যাওয়ার চিন্তা প্রভাময়ী করতে পারতেন না। পুলিন-নলিনও তা চায়নি। তাদের সংসারে অস্বচ্ছলতা কোথাও ছিল না, বরং ঠাকুরদা এবং বাবা যা রেখে গেছেন তা যথেষ্ট, ভদ্রভাবে জীবন কাটাবার পক্ষে অপ্রতুল নয়। তা ছাড়া পুলিন এবং নলিন এই শহরেই বসবে এ তারা বরাবরই স্থির করে রেখেছিল। জন্মাল এখানে, মানুষ হল, লেখাপড়া শিখল, ঘরবাড়ি থাকল এখানে—আর তারা যাবে পাটনা কি ভাগলপুরে প্র্যাকটিস শুরু করতে! দূর…তা কি হয়। পুলিন ভাল করেই জানত সে একেবারে সাধারণ ছেলে, তার এমন কোনো মেধা নেই যে, বাইরে গিয়ে চেম্বার খুললেই রাতারাতি সে পশার জমিয়ে ফেলবে। বিলেত থেকে একটা ডিগ্রি ডিপ্লোমা আজকাল কে আর না আনছে! ওটা কিছুটা শখ, কিছুটা ফালতু। তার চেয়ে এই শহরে চোখের ডাক্তার নেই, চেম্বার খুললে এখানেই খুলবে। বাবা যা চাইতেন, মা যা চায়। নলিনেরও মনোভাব সেই রকম। দাঁতের ডাক্তারও তো নেই এখানে, অথচ দাঁতের গোড়া কার না ফুলছে—এইখানেই সে প্র্যাকটিস করবে, কম্পিটিটার নেই।
পুলিন বিলেত থেকে ফিরে এসে সদর বাজারের কাছাকাছি ওদেরই এক ভাড়া দেওয়া বাড়ি মেরামত করাল, বাহারি করল। ওপরতলায় খান চারেক ফালি-ফালি ঘর থাকল, সেটা হল ক্লিনিক। নীচের তলায় দুই ভাইয়ের চেম্বার, আলাদা আলাদা, একটা আই স্পেশ্যালিস্ট ডাক্তার পি সেন-এর, অন্যটা ডেন্টাল সার্জন ডাক্তার এন সেন-এর।
পুলিন আর নলিন একেবারে পিঠোপিঠি ভাই, বছর দেড়েকের ছোটবড়। মাথার ওপর ছিল দিদি, তার বিয়ে হয়েছে মুঙ্গেরে, ভগ্নিপতি কলেজে কেমিস্ট্রির প্রফেসার। আসা-যাওয়া আছে। অতি রসিক-পুরুষ। পুলিন নলিনের বিয়েতে ভদ্রলোকের কিছুটা কারসাজি ছিল।
ওদের বিয়ের গল্পটা প্রসঙ্গত কোনো সময়ে আসবে, আপাতত এইটুকু মাত্র জানা দরকার—পুলিনের স্ত্রী মানসী, এবং নলিনের স্ত্রী সরসী সহোদর বোন, পুলিন নলিনের মতনই পিঠোপিঠি। চারজনের সম্পর্কটা তাই আরও কৌতুকপ্রদ হয়ে উঠেছে। পুলিন অনেক সময় ছোট ভাইয়ের স্ত্রীকে শালী সম্পর্কে ঠাট্টা করে, এবং নলিনও প্রত্যুত্তরে পুলিনের বউকে বড়শালীর প্রাপ্য খোঁচাটুকু মারতে ছাড়ে না।
বিয়ে হয়েছে বছর পুরতে চলল, অথচ দুই ভাই এমন সব কীর্তি করে যাতে মনে হয় এরা সদ্য বিবাহিত। যেমন আজ সকালে ফোন নিয়ে করল। এ-রকম নিত্যই হয়। চেম্বারে এসে রুগি না থাকলেই যে যার বউকে ফোনে ডেকে গল্প করতে চাইবে। মুশকিল এই, চেম্বারে পুলিনের নিজের ফোন আছে, নলিনেরও আছে; অথচ বাড়িতে মাত্র একটা ফোন। পুলিন-মানসী বাক্যালাপ চলতে থাকলে নলিন লাইন পায় না, নলিন-সরসী বাক্যালাপ চলতে থাকলে পুলিন হাঁ করে বসে থাকে। এবং দুজনেই দুজনের আক্কেল দেখে বোধ হয় অবাক হয়ে যায়।
তিন
বারোটার পর পুলিন গায়ের কোটটা কাঁধে ঝুলিয়ে শিস দিতে দিতে নলিনের চেম্বারে এসে ঢুকল। ছিপছিপে-চেহারা পুলিনের, গায়ের রং ফরসা, মুখ লম্বা ধরনের, সোজা শক্ত নাক, চোখ দুটো চকচকে, মাথার চুল কোঁকড়ানো। বাবার মুখের আদল পেয়েছে বড় ছেলে। ঘরে ঢুকে পুলিন বলল, “কই রে, তাড়াতাড়ি নে। ⋯খিদে যা পেয়েছে!⋯তোর সিগারেটের প্যাকেটটা কই⋯?” পুলিন নলিনের টেবিল হাতড়ে সিগারেট খুঁজতে লাগল।
সামান্য আগে নলিনের এক রুগি বিদায় নিয়েছে, নলিন সাবানে হাত ধুয়ে তোয়ালেতে হাত মুছছিল। হাত মোছা হয়ে গেলে—একপাশে রাখা স্টেরিলাইজার যন্ত্রপাতির বাক্সটা কাচের আলমারির মধ্যে সরিয়ে রাখল।
নলিন বেশ গোলগাল, গায়ের রং পুলিনের চেয়েও ফরসা। নলিনের মুখও গোল, ফোলা ফোলা গাল নাক একটু পুরু, চোখ দুটো স্বচ্ছ ও সুন্দর, মাথায় সাবেকি ধরনের টেরি, চোখে ক্যারেট গোল্ড ফ্রেমের চশমা; নলিন হাসলে তার দাঁত দু পলক তাকিয়ে দেখার মতন। দাঁতের ডাক্তার বলেই বোধ হয় নিজের দাঁত দেখিয়ে নলিন অনেক রুগিকে পরোক্ষে ঘায়েল করে। নলিনের মুখের আদলে মায়ের মুখের ছাপ আছে।
পুলিন সিগারেট খুঁজে ধরিয়ে নিয়েছিল। সিগারেট ধরিয়ে টানতে টানতে কি ভেবে সে দাঁত-দেখানো চেয়ারে এসে বসে পড়ল। বসে বলল, “এই দেখ তো, দাঁতের ফাঁকে কোথায় একটা কাঁটা আটকে আছে, বের করে দে।”
নলিন বিন্দুমাত্র গরজ দেখাল না। জানলার কাচের পাল্লা বন্ধ করে পরদা টেনে আলো আড়াল করে দিল।
পুলিন বলল, ‘কি রে, কাঁটাটা বের করে দিলি না?’
নলিন তার টেবিল থেকে সিগারেটের প্যাকেট কুড়োতে কুড়োতে জবাব দিল, “ওবেলা দেব। এক সঙ্গে।”
“একসঙ্গে।”
“দুপুরে গিলতে গিয়ে আবার তো একটা কাঁটা ঢোকাবি।”
পুলিন ঘাড় ফিরিয়ে ভাইকে দেখছিল, এবার উঠল। পুলিন প্রায়ই খেতে গিয়ে দাঁতের ফাঁকে কাঁটা আটকে ফেলে, নাকি আটকে যায়। তার একটু তাড়াতাড়ি খাওয়া অভ্যেস, মাছের কাঁটা বাছাও তার সহ্য হয় না। নলিন তাকে খোঁচা দিল আর কি! দিক।
ক্লিনিকের বাইরে শীতের রোদে ওদের গাড়িটা দিব্যি রোদ পোয়াচ্ছে। ছোট্ট একটা হিলম্যান, টকটকে লাল রং। পুলিন নলিন এগিয়ে গেল, চাকর চেম্বারের দরজা জানলা বন্ধ করছে, শব্দ শোনা যাচ্ছিল।
গাড়িতে উঠে পুলিন বলল, “শেতলদার মার ছানি কাটতে হবে, বুঝলি।”
নলিন অন্য পাশ দিয়ে উঠে পুলিনের পাশে বসল, “কেটে ফেল।”
নলিন এমন সাদামাটা নিরুত্তাপ গলায় বলল যে, পুলিনের মনে হল ব্যাপারটা নলিন অবহেলার চোখে দেখছে। গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে পুলিন বলল, “এ তোর দাঁত তোলা নয়, সাঁড়াশি ধরে মারলাম টান, বেরিয়ে গেল জান-প্রাণ…।”
গাড়ি চলতে শুরু করল। নলিন জবাব দিল, “হাতুড়ের মতন কথা বলিস না। দাঁতের তুই কী জানিস?”
“যা যা, দাঁতের আবার জানা⋯ ! তোরা যে কত ব্লাফ দিস লোকে তো আর জানে না। জানলে কাছে ঘেঁষত না।”
“তোরাও ঘর অন্ধকার করে যে ম্যাজিক দেখাস তাই বা ক’জন জানে বল? বুদ্ধু হয়ে টাকা গুনে দিয়ে চলে যায়।”
রাস্তায় কে একজন হাত তুলে কিছু বলল, পুলিন মাথা নাড়ল, নলিনের কথা যেন শুনতেই পায়নি। জয়মলরামের দোকান পেরিয়ে গেল, বাজারের একটা রাস্তা এখানে এসে দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে, পুলিন বাঁদিকে পথ নিল, ম্যাকসাহেবের বেকারি, মোটরবাইক দাঁড় করিয়ে হালদারদা কার সঙ্গে যেন গল্প করছে, পুলিন নলিনকে দেখে হাসল, ওরাও প্রত্যুত্তরে হাসিমুখ করল, তারপরই গণেশ হালুইকরের মিষ্টির দোকান পড়ল ডানপাশে।
পুলিন গাড়ি দাঁড় করাল। বলল, “দই নিয়ে আসবি?”
“শীতকালে দই খেতে নেই⋯”
“দইয়ের কথা বলেছিল; কি-যেন বলল আরও একটা মনে পড়ছে না।”
“আমায় কিছু বলেনি।”
“মানসী আমায় বলেছে।”
নলিন অগত্যা হাত বাড়িয়ে গাড়ির দরজা খুলল। “টাকা দে।”
“তুই নিয়ে আয়⋯”
“বেশ আছিস—”
পুলিন হাসল, বলল, “গাড়ির তেল কিনতে হবে, আমার কাছে তেলের টাকাটা আছে।”
“সকালে কিছু ইনকাম হয়নি তোর?”
“দূর⋯র। প্রথমে এল সেই ফেরিঅলা বুড়োটা তারপর এল শেতলদা। টাকা দিতে চেয়েছিল, ওকি আর নেওয়া যায়!”
নলিন দু-মুহূর্ত বড় ভাইকে দেখে গাড়ির খোলা দরজা দিয়ে নেমে পড়ল। দু-পা এগুতেই শুনল পুলিন সিগারেট-সিগারেট করে চেঁচাচ্ছে। নলিনের হাসি পেল। তাদের দুই ভায়ের পক্ষে এখানে চেম্বার খুলে বসা বোকামি হয়েছে। অর্ধেক লোকের কাছে তারা টাকা নিতে পারে না। এত সব চেনাশোনা, কেউ দাদা, কেউ কাকা-মামা, কেউ আসে বাচ্চা ছেলেমেয়েকে দেখাতে, কেউ মা-পিসিকে নিয়ে। কেউ বা নিজের জন্যেই আসে। এদের বেশির ভাগই দু-পাঁচ টাকা দিতে চায়, স্বেচ্ছায়, পুলিন-নলিন নিতে পারে না। নিতে লজ্জা করে। এভাবে কতদিন প্র্যাকটিস চলবে? নিতান্ত বাপ-ঠাকুর্দার পয়সা ছিল তাই চলছে, নয়ত মুশকিলে পড়তে হত। অবশ্য নলিন ভাবল, তারা এখন একেবারে নতুন; পুরানো হলে ফ্রি-রুগি কমে যাবে, আশপাশ থেকে দেদার রুগি আসবে।
দই কিনে নলিন দেখল টাটকা বালুসাই তৈরি হয়েছে। ফুলটুসি বালুসাই খেতে খুব ভালবাসে। নলিন বালুসাই কিনল। হালুইকরের দোকান থেকে বেরিয়ে এসে গেল পানের দোকানে, সিগারেট কিনল। গাড়িতে ফিরে আসার সময় নলিন হিসেব করে দেখল, তার সকালের রোজগার শেষ হয়ে দু-টাকা গাঁট-গচ্চা গেছে। মন্দ নয়!
গাড়িতে এসে বসে দরজা বন্ধ করল নলিন।
পুলিন শুধোল, “ওটা কী আনলি?”
“বালুসাই।”
পুলিন হেসে বলল, “সরসী বলেছিল?” বলে গাড়িতে স্টার্ট দিল আবার।
“না, তোর মতন আমার চেম্বারে বসে বসে বউয়ের অর্ডার নিতে হয় না।”
গাড়ি চলছে। পুলিন ভাইকে দেখল মুখ ফিরিয়ে। হাসছিল। শিস দিল একবার। তারপর মুখ গম্ভীর করে বেসুরোভাবে গাইতে লাগল, “যৌবন সরসী নীরে…।”
নলিন গম্ভীর হয়ে বলল, “বাড়িতে তোর শোবার ঘরে আরও একটা লাইন করিয়ে নে ফোনের। এ-রকম আর চলবে না। ফেড আপ হয়ে গিয়েছি।”
জবাবে পুলিন বলল, “তুই-ই বরং একটা করিয়ে নে, আমার তো লজ্জাই করে।”
নলিন পুলিনের মুখের দিকে তাকাল। “বাজে কথা বলিস না। আমি দেখেছি, যখনই ফোন করতে গেছি বাড়িতে তুই মানসীর সঙ্গে গল্প করছিস।”
“আমি তো দেখেছি, ঠিক উল্টো, তুই সরসীর সঙ্গে গল্প করছিস।”
“লায়ার।”
পুলিন হাসতে লাগল। সামান্য দূরে পেট্রল পাম্প। পেট্রল নিতে হবে গাড়িতে। পুলিন রাস্তার ধার ঘেঁষে পেট্রল পাম্পের দিকে এগুতে লাগল।
দুপুরের খাওয়াটা সাবেকি ধরনের। দুই ভাই খেতে বসে এক সঙ্গে, বউরা বসে না। কাছে থাকে। মা-ই সব দেখাশোনা করেন। বউরা ফরমাশ খাটে। রাত্রে অবশ্য মা থাকেন না, দুই ভাই এবং দুই বউ টেবিল ঘিরে বসে ঘণ্টাখানেক ধরে খায়। খাওয়ার চেয়ে গল্প-গুজবই বেশি করে, হাসিঠাট্টার পাট সহজে মিটতে চায় না।
পুলিন নলিন খেতে বসেছে, মা সামনে, মানসী এবং সরসী হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে আছে।
প্রভা শুধোলেন, “কই মাছটা কেমন খাচ্ছিস? নটু কোথথেকে যোগাড় করে এনেছে।”
পুলিন বলল, “কে রেঁধেছে?”
“ছোট বউমা।”
“মন্দ না⋯” পুলিন সামান্য মুখ তুলে একবার ভাই এবং পরে সরসীকে দেখে নিল। গম্ভীর হয়ে বলল, “শীতের কই এমনিতেই খেতে ভাল লাগে। ⋯তা কই মাছ রাঁধে দিদি⋯”
“কার দিদি?” নলিন সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলল।
পুলিন সামান্য অপ্রস্তুত। “কার দিদি মানে? আমাদের দিদি।”
“ও!” নলিন ঘাড় নাড়াল বার কয়েক, বলল, “আমি ভেবেছিলাম তুই সরসীর দিদির কথা বলছিস।”
সামান্য তফাতে দাঁড়িয়ে সরসী ও মানসী চোখ চাওয়া-চাওয়ি করল। হাসি চাপল।
পুলিন অল্পের জন্যে দমে গেলেও ত্বরিতে সামলে নিল। বলল, “তোর ভাবাভাবি ওই রকমই। বুদ্ধি বলে জিনিসটা তো কোনো কালে হল না। নিরেট।”
“তোর ব্রেনের ওয়েট কত?”
“যতই হোক, তোর চেয়ে বেশি।”
“তা হলে ওটা ব্রেন নয়, ব্রেনগান।”
সরসী জোরেই হেসে ফেলল। মানসী ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে হাসছিল।
পুলিন মার দিকে তাকাল। প্রভা বুঝুন না বুঝুন, হাসছিলেন। এটা নিত্য দিনের ঘটনা। এ যদি বলে ‘তুই গাধা’, ও বলবে ‘তুই এল্ডার গাধা’।
“মা, তোমার ডেন্টাল সার্জনকে বলো দাঁতের পাটি সব সময়ে চোখের তলায় থাকে।”
পুলিন বলল, “ভগবানই মেরে রেখেছেন, আমার হাত নেই।”
“ও তোর ছোটই—” প্রভা বললেন।
“ব্যবহার দেখে তো মনে হয় না। ⋯বড় ভাইয়ের বউকে নাম ধরে মানসী বলে। আস্ত একটা ছোটলোক।”
নলিন এক মনে খেয়ে যাচ্ছে, হাসিটা চোখে জড়ানো।
মানসী বলল, “হ্যাঁ মা, এটা আমিও বলব। বাইরের লোকের সামনেও ও এইভাবে ডাকে।” বোঝাই যায় মানসী ইচ্ছাকৃতভাবে নলিনকে খোঁচাবার চেষ্টা করছে।
প্রভা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই নলিন বলল, “বাইরের লোকের সামনে তোমায় কি বলে ডাকব, যদি বলো ‘মা জননী’ বলতে পারি।”
সরসী খিল খিল করে হেসে উঠল। প্রভাও হাসলেন। পুলিনও হেসে ফেলল। মানসী অপ্রস্তুত।
নলিন পুলিনকে বলল, “খাবার সময় বেশি কথা বলিস না ধীরে সুস্থে কাঁটা বেছে খা। কই মাছ খাচ্ছিস তো, সামলে⋯”
মানসী তার অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়ে উঠেছিল। নলিনকে চোখের ইশারায় কি যেন বুঝিয়ে শাসাল। নলিন সঙ্গে সঙ্গে অন্যরকম মুখ করে চোখে চোখে বলল, খবরদার।
প্রভা বললেন, “পরশু সকালে বেয়াই-মশাই আসছেন, শুনেছিস?”
পুলিন এবং নলিন দুইজনে মার মুখের দিকে তাকাল। তারা শোনেনি। শোনার অবসর হয়নি। চেম্বার থেকে ফিরে সোজা স্নান করতে গেছে, স্নান সেরে খেতে এসেছে। ইতিমধ্যে মানসী অথবা সরসীর সঙ্গে তাদের দেখা হয়েছে বুঝি একবার, কিন্তু খবরটা তখনও পাওয়া যায়নি।
“হঠাৎ ?” পুলিন শুধলো।
“যাবেন গয়া। যাবার পথে এখান থেকে ঘুরে যাবেন।”
“গয়া কেন? কার পিণ্ডি⋯না, মানে কে থাকে গয়ায়?”
“মেসোমশাই—” মানসী বলল, “মেসোমশাই অনেক দিন ভুগছেন অসুখে, দেখতে যাবে বাবা।”
পুলিন বলল, “রাত জেগে ঠাণ্ডা লাগিয়ে আসছেন কেন? মুঙ্গের থেকে দিনের বেলায় গাড়ি পাওয়া যায়।”
জবাব দিল সরসী। “বাবা রাত্তিরের গাড়িই পছন্দ করে।”
পুলিন জল খেল, ঢেঁকুর তুলল, বলল, “একলাই আসছেন নাকি?”
“একাই”, মানসী জবাব দিল।
“ন্যাচারেলি। ⋯তোপের মুখে বসে কেই বা আসতে চাইবে।” নলিন গম্ভীর মুখে বলল।
সরসী মানসী ভ্রূকুটি করে কিছু বলবার আগেই নলিন উঠে পড়ল। পুলিনও।
বিকেলে আবার চেম্বার। শীতের বেলা, পাঁচটাতেই অন্ধকার হয়ে যায় বলে পুলিন নলিন চারটে নাগাদই চলে আসে চেম্বারে। সকালের চেয়ে বিকালের দিকটাতেই লোকজন বেশি, মানে দশ বিশজন নয়, হরেদরে চার পাঁচটা রুগি। কোনো কোনোদিন ফাঁকাও যায়।
পৌষ মাস, শীতটাও বেশ পড়েছে। সাতটা নাগাদ নলিন তার কাজকর্ম শেষ করে পুলিনের চেম্বারে ঢুকল। পুলিন টেবিলে পা তুলে দিয়ে জার্নালের পাতা ওলটাচ্ছিল।
নলিন বলল, “তোর হল? আর আসবে কেউ?”
হাতের কাগজ রেখে পুলিন বলল, “না। সাতটা বাজল, চল উঠি।” বলে পুলিন তার হাতের কাছের জিনিসগুলো গুছোতে লাগল। গুছোতে গুছোতে বলল, “চন্দ্রবাবু তাঁর ভাগ্নিকে এনেছিল, বুঝলি, গ্লুকোমা বলে মনে হচ্ছে। সিরিয়াস কিছু নয়, তবু এ-বয়সে জেনারেলি গ্লুকোমা হওয়ার কথা নয়।”
“সারিয়ে ফেল।”
“সেরে যাবে। ওষুধ দিয়েছি।”
“আজ আমার একটা সাংঘাতিক এক্সপিরিয়ান্স হয়েছে।” নলিন তার সেই অভিজ্ঞতা স্মরণ করে বিভীষিকা দর্শনের ভঙ্গি করল। “একটা কাবলিঅলা এসেছিল—।”
“কাবলি⋯!” পুলিন এমনভাবে বলল, যেন কাবলিঅলাদের দাঁতে রোগ হয় এ তার জানা ছিল না।
নলিন ভাইয়ের দিকে তাকাল। “বাঃ, কাবলিদের কি দাঁত থাকে না!”
“হয়েছিল কী ওর?”
“দাঁত তুলতে হল।”
“কটা?”
“একটাই তুললাম। একটা দাঁত তুলতে ঝাড়া এক ঘণ্টা। বেটা কিছুতেই পুরো মুখ খুলবে না প্রথমে। ভুলিয়ে ভালিয়ে হাঁ করালাম তো মুখের মধ্যে কিছু ঢোকাতে দেবে না। তাতেও বাগ মানালাম তো মাড়িতে ইঞ্জেকশান করার আগেই গলগল করে ঘামতে লাগল। ওই চেহারা ভয়ে কাঠ। তারপর বেটার কী কান্না।”
“দাঁত তুললি?”
“দিলাম তুলে। বললাম, এটা তুলে দিলেই আর একটা গজাবে।” নলিন হাসতে লাগল। “অদ্ভুত, বুঝলি। নতুন দাঁত গজাবে শুনে বেটা কাবলি কাবু হয়ে গেল। ⋯ভাবল আসলটা যাক সুদ আসবে। বাপস, যা ট্রাবল দিয়েছে।”
“ক’টাকা নিলি?”
“টেন।”
“বি কেয়ারফুল। ⋯ওই কাবলি আর ক’দিন পরেই তোর চেম্বারে এসে লাঠি ঠুকবে। হামারা দাঁত কাঁহা? দাঁত দো।”
নলিন গলা ছেড়ে হেসে উঠল।
বাড়ি ফিরতে দেরিই হয়ে গেল সামান্য। শীতটাও আজ গায়ে লাগছে। বিকেল থেকেই কনকনে ভাবটা বোঝা যাচ্ছিল, শুকনো অথচ বরফকুচির মতন ঠাণ্ডা আস্তে আস্তে জমছে। জমতে জমতে এই প্রথম রাত্তিরে শরীরে কাঁটা ধরিয়ে দেবার মতন শীতল হয়ে গেছে। নাক মুখ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল, হিম পড়ছে খুব।
পুলিনের ইচ্ছে ছিল একটু খেলা হোক। বাড়ির সামনে বাগানে ঘাসের লনে তাদের ব্যাডমিন্টন কোর্ট, আলোর ব্যবস্থা আছে, নেট টাঙাবার খুঁটি আছে। প্রায়ই দুই ভাই দুই বউ নিয়ে র্যাকেট হাতে নেমে পড়ে। শরীর চর্চা তো বটেই তার সঙ্গে আনন্দ চর্চাও।
চায়ের পাট শেষ হলে (এ-সময় একবার চারজনে বসে চা খায় ওরা) মানসী বলল, “না আজ আর খেলতে পারব না, যা ঠাণ্ডা।”
পুলিন বলল, “একটু ছোটাছুটি করলেই গা গরম হয়ে যাবে।” মানসী মাথা নাড়ল। “না। সরসীর শরীরটাও ভাল নেই।”
সরসী দিদির দিকে তাকাল। মুখে আতঙ্ক ও গোপন মিনতি।
পুলিন বলল, “কী হয়েছে?”
সরসী অন্য দিকে তাকাবে ভেবেছিল, সে চাইছিল না তার মুখের ভাবটা দাদার চোখে পড়ে, কিন্তু সরসী অন্য দিকে না তাকিয়ে সোজা নলিনের দিকে তাকাল।
পুলিন কিছু বুঝতে পারল না।
জবাব দিল মানসী। বলল, “হয়েছে কিছু। শরীর খারাপ হবে না, বাঃ রে—! ও খেলতে পারবে না। আমিও বাবা এই ঠাণ্ডায় বাইরে যেতে পারব না।”
অগত্যা পুলিন তাস খেলার প্রস্তাবটা পাড়ল।
“চলে এসো—” নলিন রাজি। “ব্রিজ না ব্রে?”
“ব্ৰে না, ব্রে আমি খেলব না। ইস্⋯সবাই মিলে আমায় হারাও।” সরসী ব্রে খেলতে রাজি না।
“তবে ব্রিজ?” নলিন তাস আনতে উঠল।
“না, আমি তোমার পার্টনার হয়ে খেলব না, তুমি খালি রাগবে আর চেঁচাবে⋯” মানসী ব্রিজ খেলবে না।
“আমি সরসীকে নিয়ে খেলব।” নলিন বলল।
পুলিন বিপদ বুঝে বলল, “ব্রিজটা থাক, বরং ফিশ হোক। পয়সা লাগাও। নলিন আজ কাবলিঅলার দাঁত তুলে দশ টাকা পেয়েছে।”
মানসী হাঁ করে নলিনের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর সারা গা মুখ কুঁকড়ে কেমন একটা ভঙ্গি করল। “ই⋯মাগো! তুমি তুলতে পারলে?”
“কেন, কি হয়েছে?”
“গন্ধ⋯! বাব্বা, যা দুর্গন্ধ⋯”
“কি করে তুমি বুঝলে দুর্গন্ধ? নাক লাগিয়ে শুঁকেছ?”
“থাক, আমাকে আর শুঁকতে হবে না।” মানসী ঠোঁট উল্টে গা বিড়োনোর ভাব করল।
পুলিন বলল, “ইডিয়েট।”
তাস এনে সাফল করতে বসল নলিন। দুই ভাইয়ের শোবার ঘরের মাঝামাঝি একটা ঘরে তারা বসে আছে। এই ঘরটাই তাদের রাত্রের আড্ডাখানা। আসবাবপত্র মোটামুটি কিছু কম নেই, মেঝেতে মোটা গালচে পাতা, সোফা-সেটির সঙ্গে একপাশে ফরাসপাতা চৌকি, দরকার হলে দু-দণ্ড কেউ গড়িয়ে নেয়, এক কোণে একটা ডোয়ার্কিনের অর্গান, বাবার আমলের, অন্য কোণে দেওয়ালে একটা হরিণের সিং-অলা মাথা, তার নীচে টেলিফোন। ঘরের দরজা জানলা, কাচের শার্সি সবই বন্ধ, ফলে ঘরটা রীতিমত আরামপ্রদ হয়ে উঠেছে।
নলিন তাস সাফল করছে দেখে মানসী বলল, “আমায় কেউ ক’টা টাকা ধার দাও।”
সরসী সঙ্গে সঙ্গে পুলিনের দিকে হাত বাড়াল, “আমার সেদিনের দু-টাকা শোধ করুন।”
নলিন বলল, “নো লোন বিজনেস। যে যার টাকা পয়সা নিয়ে এসো।”
“বারে, আমি দু-টাকা সেদিনের পাই—”
“সে পরে নেবে, এখন গাঁট থেকে বের করো।”
“একই হল, আমাদের কি আলাদা গাঁট, তোমাদের সঙ্গেই গাঁটছড়া বাঁধা—” বলে মানসী বোনের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল, তারপর পুলিনের দিকে তাকিয়ে বলল, “দাও, আমাকেও দুটো টাকা দাও।”
“বাক্যেন মারিতং জগৎ—” নলিন মন্তব্য করল।
পুলিন পকেট থেকে টাকা বের করে মানসী ও সরসীকে দিল, বলল, “আমার প্রথমেই চার টাকা গচ্চা। বেশ আছো!”
তাস খেলা শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রথম দিকে তেমন একটা কলরব শোনা যায় না, গল্প-গুজব এবং তাস একই সঙ্গে চলতে থাকে; তারপর ক্রমশই এদের হইচই বাড়ে। প্রভাময়ী সন্ধের পর এদিকে থাকেন না, তাঁর নিজের ঘরে নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। অবশ্য তাঁর কাজ বলতে জপতপ ধর্মগ্রন্থ পাঠ। কোনো কোনোদিন পাড়ার কোনো প্রবীণা আসে তাঁর সঙ্গে গল্প করতে। বউদের ডাকাডাকির প্রয়োজন তাঁর বড় একটা হয় না। তিনি এদের চারজনের আনন্দের মাঝখানে ব্যাঘাত ঘটাতে চান না। বরং এই সময়টা নির্জনতা ও শান্তিই তাঁর পছন্দ। এক একদিন বউরা কিংবা ছেলেরা তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে এ সময় যেতে যেতে শুনেছে মা গুন গুন করে কীর্তন গাইছেন। প্রভার গলাটি যে এককালে অতি সুমিষ্ট ছিল তা ছেলেরা জানে, বউরাও এখন জেনে নিয়েছে।
খেলা চলছিল। মানসীর আজ কপাল ভাল। জিতেই যাচ্ছে। নলিন একবার মাত্র জিতেছে। এই দানটা কাউকে আর তাস ফেলতে সময় দিল না মানসী, হুট করে প্রায় টাকা খানেক জিতে নিল।
নলিন মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর মানসীর দিকে তাকিয়ে বলল, “কার মুখ দেখে উঠেছিলে আজ একটু বলবে।”
“কেন বলব…” মানসী পয়সার হিসেব করতে করতে জবাব দিল।
“বললে আমাদের দুই ভায়ের উপকার হত। ভোরে উঠেই সোজা চোখ বুজে তার কাছে চলে যেতাম।”
“সে আছে; তুকতাক করা মুখ। ⋯” মানসী চোখের পাতা টান করে রঙ্গভরে হাসল।
পুলিন গম্ভীর হয়ে বলল, “সেই মুখটা আমার। তুই আমার কাছে আসিস, আমি শুয়েই থাকব।”
মানসী হেসে উঠল। সরসী হাসতে হাসতে পুলিনকে বলল, “আর আপনি নিজে যে হারছেন⋯”
“নিজের মুখ নিজে নিজে তো আর দেখা যায় না, তাই।”
“বালিশের পাশে একটা আয়না নিয়ে শুবি—” নলিন জবাব দিল।
চারজনেই হেসে উঠল। পুলিন সিগারেট ধরাল। সরসী তাস দিতে লাগল।
মানসী এবং সরসীর মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই চেহারায়। মুখের আদল প্রায় এক, দুজনের মুখের ছাঁচই বটপাতার মতন অনেকটা; কপাল পুরন্ত, চিবুক সুডৌল। মানসীর গায়ের রং সামান্য মরা, চোখ দুটিও ঈষৎ বড়। মানসীর নাক তেমন উঁচু নয়। সরসীর নাক উঁচু, চোখ দুটি টলটল করছে। দুটি মুখেই প্রসন্নতা ও তৃপ্তি দেখে মনে হয় কে যেন প্রসন্নতা ও তৃপ্তির হাসির একরকম মোম ওদের মুখে মাখিয়ে এক মসৃণতা সৃষ্টি করেছে।
পুলিন একটা তাস তুলে নিয়ে দেখল, এবং মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে শিস দিল।
নলিন আপত্তি জানাল, “শিস দেওয়া চলবে না⋯”
“কেন, কেন?” পুলিন কৈফিয়ত তলব করল।
“মানসী এবার হাত ফেলে দেবে। তুমি ওকে জানিয়ে দিলে। ওটা বেআইনি।”
“তোমরাও ফেলে দাও।”
নলিন ততক্ষণে তাস টেনে নিয়ে দেখেছে, তাসটা হাতে রেখে বলল, “মামার বাড়ি আর কি! চলে এসো।”
সরসী বলল, “শিস দেওয়া কিন্তু সত্যিই চলবে না। ⋯বাবা শিস শুনলে রেগে আগুন হয়ে যায়।”
মানসীও বোনকে সমর্থন করল, বলল, “সত্যি, শিস দেওয়া যে কি বিশ্রী অভ্যেস তোমার! যতসব অসভ্যতা শিখেছ!”
পুলিন নলিনের দিকে তাকাল, তারপর মানসী ও সরসীর দিকে, “তোমার বাবা কোন ঘরে থাকবেন?”
“কেন?” দু-বোন একই সঙ্গে জানতে চাইল।
“সেই বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে। উনি ওপরে থাকলে আমায় নীচে দিও; আমার নেচারের সঙ্গে কোনো সাইলেন্সার ফিট করা নেই কিনা!” পুলিন রঙ্গ করে বলল।
মানসী সরসী দু’জনেই ঘাড় সোজা করে বসল। মানসী বলল, “গুরুজন নিয়ে তামাশা—”
“মোটেই নয়,” পুলিন মাথা নাড়ল, “আমরা হইচই চেঁচামেচি করে শিসফিস দিয়েই বাড়িতে থাকি। দুম করে স্বভাব পালটাব কি করে!”
“পালটাবে—” মানসী আদেশ জারি করার মতন করে বলল, “পালটালে মরে যাচ্ছে না কেউ।”
“না—মোটেই না⋯” বলতে বলতে নলিন হাতের তাস ফেলে দিল। পুলিন ভেবেছিল দানটা জিতবে, নলিন মেরে দিল। অনেকগুলো পয়সা। দীর্ঘশ্বাস ফেলল পুলিন।
পয়সা বুঝে নিয়ে নলিন তাসগুলো সরসীর দিকে এগিয়ে দিল। সিগারেট ধরাল আরাম করে। তারপর মানসীর দিকে তাকিয়ে বলল, “তুমি পালটানোর কথা বলছিলে, পুলিন বলছিল পারবে না। ⋯ওকে একবার মনে করিয়ে দাও না, বিয়ের কনে পালটে যাওয়ায় ওর কোনো আফশোস হয়েছে কি না!”
পুলিন ঠিক এই ধরনের একটা জবাব আশা করেনি, কেমন হকচকিয়ে গেল, অপ্রস্তুত সামান্য, তারপর কয়েকবার ‘যাঃ যাঃ’ করল। সরসী এবং মানসী দুজনেই হাসতে লাগল।
ঘটনাটা চারজনেরই জানা, কৌতুক অনুভব করতে বাধা পেল না কেউ।
মুঙ্গেরে দিদির কাছে গিয়েছিল পুলিন-নলিন। সরসীকে নয়, সরসীর ছবি দেখেছিল মুঙ্গেরের মহিলা সমিতির ছবিতে, দিদি সেই সমিতির পাণ্ডা। ছবি দেখে পুলিনের মনটা কেমন এলোমেলো করছিল। নলিনকে বলল, এ-রকম একটা মেয়ে হলে বিয়ে করা যায়। নলিন মেয়ের খোঁজ করতে গিয়ে দেখল, সরসীরা দু-বোন, সরসী ছোট। নলিন সরসীর সঙ্গে আলাপ করে ফেলল—, জামাইবাবু সহায় হলেন। মনে ধরে গেল সরসীকে। কিন্তু পুলিন?
নলিন ভাইয়ের মনটা প্রথমে আঁচ করে নিল ভাল করে, গুরুতর কিছু কি না, দেখল সে-সব নয়। তারপর বলল, ‘দেখ, মুশকিলটা কি জানিস! ওরা দু-বোন, ওই মেয়েটা ছোট। বড়টা আরও ফাইন। ওদের বাবা আবার একই সঙ্গে দুটোর বিয়ে দিতে চায়। তা তুই যদি ছোটটাকে করিস, আমায় বড়টাকে করতে হয়। সেটা কি ভাল দেখাবে! লোকে বলবে কি, ছোট ভাই বড় বোনকে বিয়ে করল! তুই যদি বলিস, আমি তোর জন্যে সেক্রিফাইস করতে পারি, নয়ত তুই বড়টাকে কর, আমি ছোটটাকে। ভেবে দেখ…।’
পুলিন বড়র ছবি চাইল দেখতে। নলিন দেখাল। বড়র গুণগানের ব্যাখ্যা সে শুধু নিজেই করল না, জামাইবাবুকে দিয়েও করাল। পুলিনের অবশ্য অত দরকার ছিল না। মানসীকে এমনিতেই তার ভাল লেগেছিল। তা ছাড়া মেয়ে দুটি তাদের বাড়ির যে যোগ্য এ-কথা দিদি বার বার বলেছে।
পুলিন দিব্যি রাজি হয়ে গেল।
নলিন বিয়ের পরই মানসী সরসীর কাছে পুলিনের মেয়ে পছন্দের গল্পটা প্রকাশ করে দিল।
পুলিন ছোট ভাইয়ের ওপর চটে গিয়েছিল, একটা ইডিয়েট; বলেছিল ‘আমি কি মেয়ে পছন্দ করেছিলুম, এমনি ঠাট্টা করে বলেছি আর—তুই সেটা নিয়ে লেগে পড়লি। আসলে ইন্টারেস্ট তোর ছিল, আমার নয়।’
‘আমার তো সেন্ট পার্সেন্ট ইন্টারেস্ট ছিল, নয়ত তোর জন্যে ওই সিক্সটি টু মডেলের জ্যান্ত কামানের সামনে কেউ দাঁড়ায়।’ সিক্সটি টু মডেল অর্থে বাষট্টি বছরের শ্বশুর।
দেখতে দেখতে রাত হয়ে এল। শীত যেন ঘরেও ঢুকেছে। তাসের পাট তুলে দিয়ে মানসী উঠল, হাই তুলল বড় করে। বলল, “বড্ড শীত, আর নয়, চলো। খেয়েদেয়ে যে যার শুয়ে পড়ি।”
সরসীও উঠে দাঁড়াল, তার বেশ ক্লান্তি লাগছে।
পুলিন আড়মোড়া ভেঙে বলল, “তোমরা বসো গে যাও, আমি একবার মার ঘর থেকে আসছি।”
চার
নির্দিষ্ট দিনে বেলা নটা নাগাদ করুণাকেতন এসে পৌঁছলেন। মেয়ে জামাইরা স্টেশনে আসতে গিয়েছিল। গাড়ির দরজা খুলে করুণাকেতন এবং তাঁর মালপত্র নামানো হল—দেখা গেল, তাঁর আকৃতির সঙ্গে তাঁর বয়ে-আনা হোন্ডঅলের আকৃতির বিশেষ কোনো তফাত নেই। লেপ, তোশক, কম্বল বালিশ যাবতীয় বিছানাপত্র ঠাসা বিপুলকায় ও খাটো মাপের হোল্ডঅলটা প্লাটফর্মে কোনো রকমে নামিয়ে কুলিরা হাঁ করে পদার্থটি অবলোকন করছিল, এবং জামাইরা দেখছিল দু-প্রস্থ জামা-জুতোর ওপর আপাদ-কণ্ঠাবৃত অলেস্টার শোভিত তাদের বেঁটে এবং গোলাকার শ্বশুরমশাইকে। গলায় মস্ত এক মাফলার তিন পাক জড়ানো, মাথায় কান-গুটানো বাঁদর-টুপি। সঙ্গে মালপত্র কিছু কম নয়, মস্ত এক সুটকেস, কপির ঝুড়ি, মিষ্টির হাঁড়ি, টিফিন কেরিয়ার, জলের কুঁজো, ছড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি।
করুণাকেতন যে বস্তুত তাঁর হোন্ডঅলের মতন নির্জীব নিরীহ নির্বাক পদার্থ নন, অবিলম্বে তা প্রকাশ পেল। মেয়ে-জামাইরা প্রণাম সারতেই তিনি দণ্ডায়মান কুলিদের দিকে তাকিয়ে তাঁর ভাঙা খসখসে গলায় চিৎকার করে ধমকে উঠলেন, “খাড়া হো কর কিয়া করতা হ্যায়, পাঁটঠা কাঁহাকার…”
তাঁর হুঙ্কার এবং মুখভঙ্গি দেখে পাঁঠারা ঘাবড়ে গিয়ে হোন্ডঅলটা টানা-হেঁচড়া করতে লাগল।
মানসী শুধল, “মা কেমন আছে?”
“যেমন থাকে,⋯” করুণাকেতন কুলিদের দেখছিলেন, “বেতো ঘোড়া।” বেতো ঘোড়া কে? মা না কুলিরা।
সরসী বলল, “বিজুর কলেজ খুলেছে?”
“দরজা খুলেছে।” মেয়েদের সঙ্গে কথা বলার চেয়ে কুলি তাড়ানোতেই তাঁর মনোযোগ।
পুলিন বলল, “আমি জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে আসছি—আপনারা এখোন।”
“আরে না না, এ তোমার বিলেত নয়; এখানকার কুলিরা লেজি, ফাঁকিবাজ, ডাকাত…। তুমি এদের সঙ্গে পারবে না।”
করুণাকেতনের বিলেত-প্রীতি না থাক, জামাইরা বিলেত-ফেরত এই অহংকার আছে। মেয়েদের বিয়েতে পাত্র অপেক্ষা পাত্রদের বিলেত-ফেরতের কথাটাই তাঁর মন টেনেছিল। তিনি এক কথায় রাজি হয়ে গিয়েছিলেন।
নলিন আড়চোখে শ্বশুরমশাইকে দেখে নিয়ে বলল, “বিলেতের কুলিরা সাহেব কুলি, এরা তো এদেশি, বেহারি-টেহারি…”
“ধড়িবাজ।” করুণাকেতন বললেন। কাকে বললেন, জামাইকে না কুলিদের বোঝা মুশকিল।
মেয়েরা তাদের বাবাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে টেনে নিয়ে চলল, পুলিন-নলিন কুলিদের দিয়ে মালপত্র গোছাতে লাগল।
নলিন বলল, “তোকে আসবার সময় বললাম, চাকায় পাম্প দিয়ে নে; নিলি না এবার…?”
“ধরবে তো সব?”
“আমি গাড়িতে যাচ্ছি না। ⋯তোরা চলে যা, আমি হেঁটে চেম্বারে চলে যাব।”
“না না, সেটা বিশ্রী দেখাবে।”
“দেখাক গে, গাড়ির চাকা খুলে মাটিতে বসে রগড়ানোর চেয়ে সেটা ভাল।”
“চল চল—যাবার সময় চাকায় পাম্প দিয়ে নেব।”
“তোমরা যাও। আমি ওর মধ্যে থাকছি না।”
“শ্বশুর কি আমার একলার? তোমারও শ্বশুর। মাইণ্ড দ্যাট—”
নলিন যুক্তিটা অস্বীকার করতে পারল না, চুপ করে গেল। পরে প্লাটফর্ম দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে বলল, “বিয়েতে আমরা এ-রকম একটা ফাউ পাব জানলে বিয়েই করতাম না।”
করুণাকেতনের অভ্যর্থনায় কোনো ত্রুটি হল না। নীচের তলায় তাঁকে মস্ত ঘর দেওয়া হয়েছিল। খাট-বিছানার অভাব থাকার কথা নয়, ঘরের মধ্যেও সারাদিন রোদ, জানলার বাইরে বাগান, ঘরের সঙ্গে লাগানো কলঘর। করুণাকেতন প্রীত হলেন। প্রভাময়ী নিজেই বেয়াইয়ের সুখ-সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্য দেখছিলেন, তাঁর কথা মতনই সব ব্যবস্থা হয়েছে। দোতলায় ওঠানামা করতে বুড়ো মানুষের কষ্ট হবে বিবেচনা করে নীচেই ব্যবস্থা করেছিলেন। মনে একটু শঙ্কা ও সঙ্কোচ ছিল, বেয়াইমশাই এই ব্যবস্থায় ক্ষুণ্ণ হন কি না। করুণাকেতন বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হলেন না, বললেন, তিনি একটু নিরিবিলি পছন্দ করেন।
করুণাকেতনের খাবার সময় মেয়েরা কাছে থাকলেও প্রভাময়ী নিজেই দেখাশোনা করলেন। কুটুম মানুষ, ব্যবস্থার কোনো রকম ত্রুটি, সুখ-সুবিধের স্বল্পতা প্রভাময়ী রাখেননি। দেখলেন, করুণাকেতন ভোজন বিষয়ে অসংযমী। খেতে ভালবাসেন। খাওয়ার গল্প করতে ভালবাসেন। এক সময় হাকিম ছিলেন, ঘুরেছেন নানা জায়গায়; কোথায় কোন খাদ্যটা পাওয়া যায়, তার স্বাদ কেমন, দাম কত এ-সবও নখদর্পণে।
“আমার হাই ব্লাডপ্রেশার⋯” করুণাকেতন নিজেই বললেন, “বেশ হাই। আমার ফ্রেণ্ড বলাই-ডাক্তার বলে খাওয়া কমাতে। আমি বলি ও-সব বুজরুকি, খাওয়া কমালে প্রেশার কমে না। তোমার তো বাপু এই দুটো আহার, তোমার প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে কেন? বলাই জবাব দিতে পারে না। বলে, বয়েস⋯। আরে, বয়েসে যা তা হবেই, মাথার চুল পাকবে, দাঁত পড়বে, ঘুম হবে না। বয়েসে যদি ব্লাডপ্রেশার বাড়ে, বাড়বে; তা বলে খাব না। ⋯মরব ভেবে খাওয়া বন্ধ রাখা আমার কুষ্ঠিতে লেখেনি।”
প্রভাময়ী প্রতিবাদ করলেন না, করা উচিত নয়, বললেন, “তা তো ঠিকই।”
দুপুরে করুণাকেতন বেশ একটা ঘুম দিলেন। ঘুম থেকে উঠেই বিপত্তিটা দেখলেন।
মুখ ধুয়ে অভ্যাস মতন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বিরলকেশ মাথাটি আঁচড়াতে গিয়ে লক্ষ করলেন ডান চোখটা একটু লাল। চোখে জল দেবার সময় সামান্য জ্বালা জ্বালা করছিল, অতটা খেয়াল করেননি। ঘুমের জন্য চোখটা লাল হতে পারে। দু’চোখের জমি বিচার করে যদিও মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল, করুণাকেতন তখনকার মতন ডান চোখ লাল হওয়াটাকে ঘুমের দরুন হতে পারে ভেবে কাউকে কিছু বললেন না।
আধঘণ্টা খানেকের মধ্যে বার দশ-বারো চোখ দেখলেন। উহুঁ, লাল ভাবটা কাটছে না।
মানসী চা এনেছিল। চা খাবার সময় মেয়েকে বললেন, “আমার ডান চোখটা দেখ তো।”
মানসী চোখ দেখল, বলল, “একটু লাল হয়ে আছে।”
“কেন?”
কেনর জবাব কি দিতে পারে মানসী। বলল, “কি জানি! চোখে কিছু পড়েছিল হয়তো।”
কোথায় কি পড়েছে মানসীর জানার কথা নয়, তবু আমতা আমতা করে বলল, “ট্রেনে এসেছ, ধুলোবালি পড়েছে হয়তো। ⋯”
“জ্বালা করছে।” করুণাকেতন বললেন, এবং ডান চোখটা একটু ছোট করে তাকিয়ে থাকলেন।
সরসী এল। সরসী আসতেই করুণাকেতন ছোট মেয়েকে দিয়ে আর একবার চোখ দেখালেন। “লাল হয়েছে—” সরসী বলল।
“টকটকে লাল?”
“না—, অতটা টকটকে নয়, তবে লালই⋯”
“কেন?”
সরসী দিদির দিকে তাকাল। মানসী কোনো সঙ্গত জবাব ইশারায় বলে দিতে পারল না। অগত্যা সরসী বলল, “ঠাণ্ডা লেগেছে হয়তো, রাত্রের গাড়িতে এসেছ।”
“কেমন করে লাগল!” করুণাকেতন বেশ দুশ্চিন্তায় পড়লেন, এবং ডান চোখ বন্ধ করে থাকলেন কিছুক্ষণ। খুললেন আবার বন্ধ করলেন। এই রকম চলতে লাগল।
মানসী বলল, “তুমি ভেবো না, ওরা চেম্বারে চলে গেছে, ফিরে এসে দেখবে।”
করুণাকেতন অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন, “যাবার সময় এখান থেকে ঘুরে যাওয়া যেত না!” মেয়েরা মুখ নিচু করে থাকল।
সন্ধে থেকে করুণাকেতন রীতিমত অধীর হয়ে চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন। ঘন ঘন আয়নায় চোখ দেখছেন, মেয়েদের দিয়ে দেখাচ্ছেন। প্রভাময়ী গোলাপজল আনিয়ে দিলেন। চোখে জল দিয়ে ঘরের সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ করিয়ে সবরকম গরম জামা-কাপড় পরে করুণাকেতন বিছানায় শুয়ে থাকলেন। ঘরের বাতিটা পর্যন্ত বদলাতে হল।
মানসী স্বামীকে ফোন করল, “একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার চেষ্টা করো। বাবার ডান চোখটা লাল হয়েছে। বড্ড অধীর মানুষ তো, চেঁচামেচি করছেন।”
“চোখ লাল !⋯খুব⋯?”
“না, না। ডান চোখ। অল্প।”
“অত চোখ লাল করলে একটু ওই রকম হয়ই…” পুলিন ঠাট্টা করে বলল।
“তামাশা কোরো না, আমার বাবা; তোমারও শ্বশুর।”
“সে আর বলতে। ⋯ঠিক আছে, আমরা আধঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ফিরব।”
বাড়ি ফিরে পুলিন-নলিন অবাক। করুণাকেতনের ঘরের আবহাওয়া যেন হাসপাতালের কেবিনের মতন করে ফেলা হয়েছে।
পুলিন চোখ দেখল শ্বশুরের। বলল, “ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি।”
“কী হয়েছে?” করুণাকেতন শুধোলেন।
“তেমন কিছু না⋯কাশিটাশি হয়েছে আপনার?”
“শীতকালে একটু আধটু কাশি হবে না?”
“না, না, জোর কাশি? দমক?”
“না।”
“ঠাণ্ডাফাণ্ডা লাগতে পারে। ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি।”
“জ্বালা করছে যে হে⋯, ব্যথা ব্যথা লাগছে।”
“মাইল্ড ইনফেকশান হতে পারে, ওষুধ দিচ্ছি সেরে যাবে।”
“কী ওষুধ?”
“বিলেতি।” পুলিন গম্ভীর হয়ে বলল।
পাঁচ
ব্যাপারটা অত সহজে মিটল না। পরের দিন সকালে করুণাকেতন নিজের চোখ দেখে মূর্ছা যান আর কি। ডান চোখের লালটা আরও ছড়িয়েছে। একেবারে রক্তের মতন টকটক করছে লাল। জামাই কি ওষুধ দিল? করুণাকেতন হাত-পা ছোঁড়া শুরু করলেন। ভয়ে বুক ধকধক করছে, মাথা ঘুরছে।
পুলিন আবার চোখ দেখল। বলল, “স্লাইট স্প্রেড করেছে। ওষুধটা দিন। বিকেলে দেখব আবার।”
মানসী আড়ালে স্বামীকে বলল, “বাবার খুব আতুপুতু আছে। একটু কিছু হলেই বাড়ি মাথায় তোলে। তাড়াতাড়ি সারিয়ে দাও বাপু। বদখেয়ালের মানুষ, মুখেরও কিছু ঠিক নেই, কখন কি বলে ফেলবে, আমি লজ্জায় পড়ব।”
পুলিন হেসে বলল, “সিরিয়াস কিছু না। কত কারণেই চোখ লাল হয়। তোমাদের মুখ যেমন লাল হয়।”
মানসী মুখভঙ্গি করে স্বামীকে ঠেলে দিল।
করুণাকেতন বিকেল থেকে আর আত্মসংবরণ করতে পারলেন না। থেকে থেকেই করুণকণ্ঠে নিজের দৃষ্টিহীনতার সম্ভাবনার কথা ঘোষণা করতে লাগলেন, মাথা চাপড়ানোও শুরু হল, ডান চোখের ওপর একটা মস্ত রুমাল চাপা দিয়ে স্বাগত-ভাষণে জানাতে লাগলেন যে, তিনি ইহজীবনের মতন একটি চক্ষু হারালেন।
মেয়েরা এবং প্রভাময়ী যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিয়েও করুণাকেতনকে সংযত রাখতে পারছিল না।
পুলিনরা বাড়ি ফিরলে মানসী সরসী বলল, “বুড়ো মানুষকে এত কষ্ট দেওয়া কেন? কি রকম যে আনচান করছেন। যা হয় করো একটা কিছু।”
প্রভা বললেন, “ওঁর কষ্ট হচ্ছে। গাল মুখও ব্যথা ব্যথা বলছেন।”
পুলিন বলল, “চোখ উঠলেও দু-চার দিন কষ্ট হয়, তার কি করা যাবে! এমন কিছু হয়নি যার জন্যে এত ব্যস্ত হচ্ছ। ⋯আজ একটা অয়েন্টমেন্ট এনেছি, রাত্রে লাগান, কাল দেখব ভাল করে।”
পরের দিন পুলিন নানারকম যন্ত্রপাতি এনে ভাল করে দেখল শ্বশুরকে। দেখতে কি দেন করুণাকেতন, সোজা তাকাতে বললে বাঁকা তাকান, চোখের পাতা ছুঁতে গেলে ধমকে দু-পা সরিয়ে দেন। ইতিমধ্যে একটা গগলস তাঁর চোখে উঠেছে। চোখের সঙ্গে গালগলারও যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল, মাড়ি ফুলেছে দাঁতের।
পুলিন কোনো হদিশ করতে পারল না, তার যাবতীয় জ্ঞান বলছিল চোখের কোথাও কিছু হয়নি। অথচ…অথচ…।
পুলিন নলিনকে বলল, “তুই একবার দাঁতটা দেখ⋯”
নলিন দাঁত দেখল এবং গোটা কয়েক ওষুধপত্র এনে দিল। “কুলকুচো করুন, এই পেন্টটা দিনে চারবার, ট্যাবলেটটা খাবার পর দুটো করে⋯।”
কিছুতেই কিছু না। যদিবা একটু কমেও থাকে করুণাকেতনকে দেখে তা বোঝার উপায় নেই। তাঁর মেজাজ এবার চড়ায় উঠে গেছে। কোনো কিছু পরোয়া করছেন না, মেয়ে জামাই বলে কোনো সঙ্কোচ নেই। প্রভাময়ীর ওপরই যেটুকু প্রসন্ন আছেন এখন পর্যন্ত।
মানসী মাথা ধুইয়ে দিচ্ছিল, সরসী সুজির পায়েস, ওভালটিন এনে গুছিয়ে রাখছিল বিছানার কাছে টেবিলে।
করুণাকেতন বললেন, “আমি কিছু খাব না। ⋯বিজুকে তার করে দাও, সে এসে আমায় নিয়ে যাক। আমি এখানে থাকব না।”
মেয়েদের মুখ লাল হয়ে উঠল। তারপর যেন কালসিটে ধরে গেল।
মানসী বলল, “তুমি এত অধীর হয়ে পড়ছ কেন? এরা তো দেখছে।”
“কারা?”
“তোমার জামাইরা⋯” মানসী রাগ করে বলল।
“ওরা জামাই না কসাই?”
সরসীর চোখে জল এল ; বলল, “ডাক্তার তো⋯বিলেতফেরত…”
“বাজে কথা। ওরা বিলেতে গিয়ে আড্ডা মেরেছে। জাল ডিপ্লোমা টাকা দিয়ে বাগিয়ে এনেছে। চিট…। ⋯ঘোড়ার ডাক্তার ওরা, বুঝলে⋯! বাঁদর—!”
সরসী আর কথা বলল না, ঘর ছেড়ে চলে গেল।
মানসীও চলে যেত, তবু গেল না, সে বড়। বলল, “বিজুকে তার করতে হবে না। মা কি ভাববেন! আমি দেখছি—”
“তুমি আমার কোনটা দেখবে! বিয়ে করে পর হয়ে গেছ। বাপ মরছে মরুক, তোমরা তোমাদের বরের আত্মসম্মান দেখছ।”
মানসীর গলা ক্ষোভে বন্ধ হয়ে গেল।
দুপুরে পুলিন নলিন বাড়ি ফিরতেই দুই বোন ঝাঁপিয়ে পড়ল। করছ কী তোমরা? কিছু না করে চারটে দিন বুড়ো মানুষটাকে অযথা যন্ত্রণা দিচ্ছ! মনে রেখো, আমাদের বাবা। তোমরা কেমন ওর জামাই? কী শিখে এসেছ বিলেতে? রোগ যদি সামান্যই হয়—তবে সারছে না কেন? ঘুম নেই, খাওয়া নেই, বুড়ো মানুষ চার দিনে কতটা কাহিল হয়েছে দেখতে পাচ্ছ না! ডাক্তার না হাতি!
পুলিন বলল, “ঠিক আছে, আজ বিকেলে আমাদের শঙ্করমামাকে ডাকি, একবার দেখে যান। ⋯ওঁর ওপিনিয়ান নেওয়া হোক।”
শঙ্করবাবু প্রবীণ লোক, এ শহরের সেরা ডাক্তার। এলেন, দেখলেন যত্ন করে। বললেন, তেমন কোনো গণ্ডগোল তো দেখতে পাচ্ছি না। প্রেশারটা বেশ হাই। ব্লাড টেস্ট করতে পারি, তবে দরকার কি! চোখ দাঁতের ব্যাপারে তোমরাই তো আছ, আমি আর কি করব। প্রেশারের জন্যে একটা ট্যাবলেট দাও।
রাত্রে পুলিন নলিনকে বলল “কমপ্লেনটা দাঁতের হতে পারে, চোখে সেপটিক ফোকাস পড়েছে। তুই দাঁতের ট্রিটমেন্ট কর।”
নলিন বলল, “দাঁতে যা করার আমি করছি, তুমি চোখ সামলাও, হেমারেজ চোখে হয়েছে, দাঁতে নয়।”
“আহা, কিন্তু সেটা তো দাঁতের জন্যে হতে পারে—”
“পারে তো অনেক কিছুই—”
“তুই একটা আস্ত ইডিয়েট। কিচ্ছু জানিস না, কোনো কিছু শিখিসনি, পড়িসনি।”
“তুমি আমার সাবজেক্টে কথা বলতে এসো না; আই নো বেটার দেন ইউ। তুমি চোখ সামলাও, আমি দাঁত সামলাব। দাঁতে মস্ত একটা কিচ্ছু হয়নি।”
“ননসেন্স—। রেসপনসিবিলিটি বলে কিছু নেই তোর।”
“বোগাস—। তোর এবিলিটি তো দেখতেই পাচ্ছি।”
শোবার ঘরে মানসী বলল, “করছ কি তোমরা⋯, বাবার স্বভাব তো জানো না। এখন ঘরে বসে গালাগাল দিচ্ছে, এরপর সকলের সামনে যাচ্ছেতাই করবে। মার কানে যদি যায়, কেলেংকারি।”
পুলিন চিন্তিত মুখ করে বলল, “ব্যাপার কি জানো। চোখের ব্যাপারে একটা মাইনর কিছু করতে পারি। কিন্তু ওই রকম হাই ব্লাডপ্রেশার, সাহস হয় না। বুড়ো মানুষ, তায় শ্বশুর, তার ওপর রিস্ক। যদি কিছু একটা হয়⋯আপদ বিপদ⋯।”
মানসী আঁতকে উঠল। সর্বনাশ! হিত করতে বিপরীত কিছু একটা হয়ে যাক, তারপর লোকে বলবে বড় জামাই শ্বশুরকে মারল। মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। ছিছি করবে সকলে। তা ছাড়া বরাবরের মতন একটা দাগ থেকে যাবে, বদনাম অপযশ, খুঁত। স্বামীর ডাক্তারিতেও নিন্দে রটবে। যে ডাক্তার নিজের শ্বশুর মারে তার কাছে কোন রোগী আসবে গো!”
মানসী পুলিনকে আঁকড়ে ধরল, বলল, “সর্বনাশ! না—না, ওসব তোমার করতে হবে না। খুনের দায়ে পড়বে নাকি!⋯দরকার নেই আগ বাড়িয়ে বিপদ ডেকে। ⋯যা করার অন্যে করুক।”
“নলিন দাঁতটা তুলে দিলেই আমার মনে হচ্ছে সব সেরে যাবে—”
“তবে কি! ঠাকুরপোই যা করার করুক, তোমার দালালি করতে হবে না। ওই নমো-নমো করে থাকো, লোশান-টোশান পর্যন্ত দাও তার বেশি নয়।”
সরসী নলিনের মধ্যেও কথাটা খোলাখুলি হয়ে গেল।
নলিন বলল, “একটা দাঁত তো ডেনজারাস হয়ে রয়েছে। তুলে দিতে পারি, তুলতে অসুবিধে নেই। কিন্তু যেরকম হাই ব্লাডপ্রেশার। তুলতে গিয়ে কোনো রকম বেকায়দা কিছু হয়ে যাক, ক্লট ফ্লট হয়ে যাক একটা, তারপর দম করে তোমার বাবা স্বর্গলাভ করুন। বাপস, ওই রকম রুগির চিকিৎসা!”
সরসী শিহরিত হল! বলে কি? এত কাণ্ড ভেতরে। না বাবা, দাঁত তুলে দরকার নেই। বলা কি যায় বিপদের কথা! এক করতে আরেক হবে। তখন লোকে বলবে, ছোট জামাই শ্বশুরকে মারল। বরাবরের বদনাম, মা ভাইয়ের কাছে মুখ দেখানো যাবে কোনোকালে। কেন বাবা, দরকার কিসের আমার পা বাড়িয়ে গর্তে পড়ে। এসব জিনিস থেকে সরে থাকা ভাল। সংসার বড় মুখ বাঁকা, একবার বেঁকলে সারাজীবন তার মুখ সোজা হয় না।
সরসী স্বামীর হাত আঁকড়ে ধরল, বলল, “আমার মাথার দিব্যি, তুমি ওকাজ করতে যেও না। মানুষ মারার দায়ে পড়বে, তাও আবার শ্বশুর। বদনাম, নিন্দে। মাগো, ভাবতেও পারি না। রুগিও জুটবে না আর কপালে। কাজ কি তোমার ফাঁসির দড়িতে হাত দিয়ে। আপনারটা সামলে থাকো…”
নলিন বলল, “আমি কি অত বোকা! পুলিন যা করার করুক, চোখ নিয়েই তো গণ্ডগোল শুরু! দাঁতের কথা কার বা খেয়াল হবে।”
সরসী বলল, “সেই ভাল। দাদা যা পাপ করবে…। তুমি গা-আলগা দিয়ে থাকো।”
অতঃপর কয়েকটা দিন মানসী পুলিনকে ও সরসী নলিনকে আগলে আগলে রাখল। কারোরই ইচ্ছে নয়, তার স্বামী এমন একটা মারাত্মক কাজে হাত দেয়। ওদের ভয় ছিল বাবা যেরকম বেপরোয়া হয়ে হইচই, চেঁচামেচি, গালমন্দ শুরু করেছেন তাতে স্বামীরা না অসহ্য হয়ে সত্যি সত্যি একটা কিছু করতে বসে। মানসী পুলিনকে আড়ালে বার বার বলত, ‘খবরদার’; সরসী নলিনকে বলত; ‘মাথা গরম করে দাঁত তুলতে যেও না।’…
দুই বোন কেউ কাউকে বুঝতে দিত না, আড়ালে তারা স্বামীদের কেমন করে সামলাচ্ছে। বরং বিরক্তিই দেখাত সামনা-সামনি। কী যে সব ডাক্তার ছাই বুঝি না। হপ্তা কেটে গেল, কোনো কিছু করতে পারলেন না। ⋯এর চেয়ে বাবার মুঙ্গেরে ফিরে যাওয়াই ভাল ছিল। বিজুকে সত্যিই একটা টেলিগ্রাম করে দি, কি বলিস!
প্রভাময়ী ছেলেদের ওপর ভরসা রাখেননি। পাড়ার প্রবীণা যারা আসত তাদের কাছে বলতেন সব। তারা নানারকম টোটকার খবর দিত। অমুকের পাতার রস, তমুকের মাজন, অমুক ঠাকুরের পায়ে ছোঁয়ানো হলুদ ভেজানো কাপড়, তমুক ফল বেটে পুড়িয়ে গরম জলে মিশিয়ে কুলকুচো⋯ইত্যাদি ইত্যাদি। প্রভাময়ী সেই টোটকা যা যা সংগ্রহ করতে পারছিলেন করুণাকেতনকে লুকিয়ে লুকিয়ে ব্যবহার করাচ্ছিলেন। করুণাকেতনও করছিলেন।
বিজুকে টেলিগ্রাম করা হল মুঙ্গেরে। করুণাকেতনের চোখে সর্বদা গগলস। সারাটা দিন ছটফট করতে করতে আর চেঁচামেচি করে করে শরীর কাহিল হয়েছে, গলা বসে গেছে। ঘরের দরজা জানলা বন্ধ থাকায় আলো বাতাস আসতে পায় না; বাতাসে বন্ধ গন্ধ ধরে গেছে।
ছয়
অবশেষে একদিন কেমন করে কী যেন হয়ে গেল। করুণাকেতন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে চোখে গগলস এঁটে কলঘরে মুখ ধুতে গেলেন। মুখে জল দিতে গিয়ে দেখলেন মুখে স্বাদ লাগছে, কুলকুচো করতে কোনো কষ্ট হল না, মাড়ি বা দাঁতের গোড়ায় ব্যথাও নেই, গাল গলা টিপলেন নিজে নিজেই—ব্যথা লাগল না। এতদিন ভয়ে গগলস জোড়া খুলতেনই না, মুখে চোখে জল দিতে হলে ডান চোখটা বন্ধ করে রাখতেন। সাহস করে আজ গগলস খুলে ভয়ে ভয়ে ডান চোখের পাতা খুলে আয়নায় চোখ দেখলেন। বিশ্বাস হল না, আবার দেখলেন ভাল করে, সর্বাঙ্গে বুঝি আনন্দের তড়িৎ খেলে গেল।
ঘরে এসে মেয়েদের ডাকাডাকি শুরু হল। মানসী ছুটে এল, সরসী এল। প্রভাময়ীও এলেন সামান্য পরে। ঘরের দরজা জানলা করুণাকেতন নিজের হাতেই মহানন্দে খুলে দিচ্ছিলেন। বিকট শব্দ হচ্ছিল। এ ক’দিন ঘরে আলো বাতাস ঢোকেনি। সকালের আলো রোদ ও বাতাসে বাসি ঘর যেন ধোয়ামোছা হতে লাগল।
করুণাকেতন মানসীকে বললেন, “দেখ…চোখটা দেখ একবার…”
মানসী দেখল। চোখের কোথাও লালের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। বলল, “লাল নেই কোথাও, পরিষ্কার একেবারে সাদা।”
সরসীকে দিয়েও চোখটা দেখালেন একবার। সরসী দেখল। বলল, “কিছু নেই কোথাও। সেরে গেছে।”
করুণাকেতন এবার দাঁত দেখলেন। না তাঁর সেই মাড়ির গোড়া আর ফুলে নেই, সাদাটে দাগ ধরে নেই ব্যথার জায়গাটাতে।
করুণাকেতন ঘরের মধ্যে নাচতে লাগলেন যেন। প্রভাময়ী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে হাসলেন।
পুলিন নলিন এতক্ষণ ভয়ে ভয়ে আসেনি, চেম্বারে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল। তারাও এল।
করুণাকেতন পুলিনের দিকে তাকিয়ে অতিশয় গম্ভীর হয়ে গেলেন, এবং নলিনকে হাতের ইশারায় কাছে আসতে বারণ করলেন।
প্রভাময়ী কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, বাধা দিয়ে করুণাকেতন কোনো রকম তোয়াক্কা না করে বললেন, “ছেলেদের বলুন, ডিসপেনসারি তুলে দিয়ে আপনার কাছে টোটকা শিখুক। ⋯ওয়ার্থলেস⋯ওই দুটোই সমান। কিচ্ছু জানে না⋯। হাতুড়ে⋯।”
পুলিন নলিন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। মানসী সরসীকে দেখল একবার আড়চোখে। বউরা কেউই লজ্জিত নয়, মুখে চোখে রাগের ভাবও দেখা যাচ্ছে না।
পুলিন কোনোরকমে বলল, “আপনি টোটকা করছিলেন?”
করুণাকেতন প্রায় ভেঙিয়ে উঠে জবাব দিলেন, “না করব না, তোমাদের জন্যে, বসে থাকব, কবে আমায় অন্ধ কর,—না?”
নলিন বলল, “আমাদের বলা উচিত ছিল…”
মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে করুণাকেতন জবাবে বললেন, “কেন? আপনারা কে? আপনাদের কেরামতি কত তা আমার জানা আছে…যত সব পেন্টুল ডাক্তার।”
পুলিন নলিন মুখ লাল করে বেরিয়ে গেল।
একটা দিন অপেক্ষা করে করুণাকেতন গয়ার গাড়িতে উঠলেন। যথারীতি সাজ-পোশাক ও মালপত্র সমেত। মেয়ে জামাইরা স্টেশনে তুলে দিতে এসেছিল।
গাড়ি ছাড়ার আগে করুণাকেতন জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে জামাইদের বললেন, “কিছু মনে কোরো না; বুড়ো মানুষ, দু-চারটে কটু কথা বলেছি। —দেখো হে, আমি দেখলাম তোমাদের একটু টোটকাও শিখে রাখা দরকার। দেশি জিনিসটা ফেলনা নয়। বিলেতিটা বাইরে দেখাবে, দেশিটা আণ্ডারহ্যাণ্ড।”
দুই জামাই একই সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, “যে আজ্ঞে—”
তারপর করুণাকেতন মানসীকে বললেন, “তোদের শাশুড়িকে বলবি নাতিকে যেন কানের ডাক্তার করে। ওটাই যা বাকি।”
মানসী ঠোঁট কামড়ে হাসি চেপে সরসীর দিকে তাকাল।
গাড়ি ছেড়ে দিল, এবং দেখতে দেখতে করুণাকেতনের মুখ অদৃশ্য হয়ে গেল।
পুলিন নলিন হাঁপ ছাড়ল। নলিন বলল, “বাপ্স⋯”, পুলিন বলল, “উন্মাদ একেবারে!”
মানসী হাঁটতে হাঁটতে বলল, “তোমাদের ক্ষমতায় কুলোলো না, এখন তো আমাদের বাবাকে উন্মাদ বলবেই—”
সরসী বলল, “লজ্জা করা উচিত।”
পুলিন প্লাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে পড়ল, বলল, “সারাবার কী ছিল, এ সিমপ্ল কেস অফ কন্জাংটিভাইটিস⋯। নিজের থেকেই সেরে যেত…। বরং দাঁতটা⋯”
নলিন বাধা দিল, বলল, “দাঁতে তেমন কিছু হয়নি, ইন ফ্যাক্ট গামবয়েল হয়ে কোথাও সেপটিক অ্যাবজরপ্শান হচ্ছিল। একটু চিরে দিলেই চলত—এমনিতেও কুলকুচো করলে পেন্ট লাগালেও অনেক সময় সেরে যায়।”
মানসী সরসী হাঁটতে লাগল। পুলিন নলিনও।
মানসী বলল, “এখন তো দুজনেই গলা বড় করে বলছ, কিছুই না, এটা সিমপ্ল সেটা সিমপ্ল, তখন এত বিদ্যে কোথায় ছিল?”
পুলিন নলিনের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে হাসল। তারপর মানসীর দিকে তাকিয়ে বলল, “আমার দোষ কি, তুমিই তো বাগড়া দিচ্ছিলে। ভাবছিলে তোমার বুড়ো বাবাকে মেরে আমি কেন দোষের ভাগী হই। মরে মরুক নলিনের হাতে…”
নলিন বলল, “সরসীও যা শত্রু পরে পরের তালে ছিল—”
দুই বোন থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কেমন সব মানুষ দেখছ? দুম্ করে সব বলে দিল। লজ্জায় মরে আর কি দু-বোনে!
ছি ছি। মাথা কাটা যাচ্ছে যেন। চটে গিয়ে মানসী বলল, “বা, এখন আমরা⋯। তুমি যে তখন বললে, ভয়ের ব্যাপার আছে…”
সরসীও নলিনকে আক্রমণ করল, “তুমি না বলেছিলে, এটা আছে ওটা আছে…দাঁত তুলতে গেলে অঘটন ঘটতে পারে…”
নলিন পুলিনের দিকে তাকাল, পুলিন চোখ টিপল। দুজনে চোরা হাসি হাসল। তারপর নলিন বলল, “ও আমরা বলেই থাকি। মানে, ইচ্ছে করেই বলেছি।”
“কেন, কেন?” দুই বোন দুই স্বামীর হাত ধরে টান মারল।
পুলিন নিশ্চিন্ত গলায় বলল, “না, মানে—এ রকম কিছু না বললে তোমার বাবা আর তোমাদের উপদ্রব থেকে রেহাই পাওয়া যেত না। বাব্বা, যা দৌরাত্ম্য!”
মানসী পুলিনের গায়ে জোর একটা ঠেলা মারল। “অসভ্য কোথাকার।”
নলিন বলল, “তোমাদের বাবা হতে পারে কিন্তু আমাদের কাছে যে ওই বাবাটিই বাঘ।”
সরসী নলিনের পিঠে এক কিল বসিয়ে দিল।
পুলিন ওভারব্রিজের সিঁড়ি উঠতে উঠতে শিস দিচ্ছিল, নলিন হাসছিল।
দুই বোনে পাশাপাশি ওভারব্রিজের সিঁড়ি উঠছিল। মানসী বলল, “দেখ, বাবা তো সব সময় চোখে গগলস দিয়ে থাকত, না হয় ডান চোখটা রুমাল দিয়ে ঢেকে রাখত। আমার মনে হয়, অনেক আগেই চোখ সেরে গিয়েছিল, দেখতে তো দেয়নি আমাদের, নিজেও দেখত না ভয়ে।”
সরসী মাথা নাড়ল; হয়তো তাই। বলল, “দাঁতের ব্যথাও ছিল না বুঝলি। আতঙ্কে ওই রকম করত। গালে ব্যথা হলে অত চেঁচামেচি কি মানুষ করতে পারে। শক্ত টোস্টই বা খেত কি করে।”
মানসী মাথা নাড়ল। ঠিক। তারপর দুবোনেই সিঁড়ি উঠতে উঠতে খিলখিল করে হেসে উঠল।
চুম্বক চিকিৎসা
মুদির দোকানে যেভাবে ফর্দ মেলায় সুবোধ ডাক্তার সেইভাবে হাতের কাগজগুলো মিলিয়ে নিয়ে গুরুপদ সান্যালকে বললেন, “বাঁচতে চাও, না, মরতে চাও?”
গুরুপদ ভিতু মানুষ। ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, “কেন? কী হয়েছে?”
সুবোধ ডাক্তার বললেন, “মানুষের পাঁচটা ইন্দ্রিয়। তোমার পাঁচটাই বরবাদ হতে চলেছে। হবে না? টাকা ছাড়া কিছু চিনলে না। হরিনামের মালার মতন শুধু টাকা টাকা জপ করে গেলে। এবার বোঝো!”
এমনিতেই গুরুপদর ঘাম-ধাত; গলগলিয়ে ঘামেন সারাক্ষণ, তারপর ফাল্গুন মাস পড়তে না পড়তেই গরম শুরু করেছে এবার। গুরুপদ ঘামতে লাগলেন। গলা শুকিয়ে গেল। বললেন, “কী হয়েছে সেটা বলবে তো?”
সুবোধ বললেন, “কী হয়নি। ব্লাড প্রেশার হাই, ব্লাড সুগার অ্যাবনরমালি বেশি, যে কোনোদিন মাথা ঘুরে পড়ে গিয়ে চোখে অন্ধকার দেখতে পারো। ব্লাড কোলেস্টরাল যাচ্ছেতাই, তার ওপর হার্ট, ওদিকে তোমার পুরনো পাইলস। কোনটা দেখব। যেদিকে দেখছি চোখ ছানাবড়া হয়ে যাচ্ছে। এত্ত সব বাধিয়ে বসেছ যে তোমার কোন চিকিৎসা আমি করব বুঝতে পারছি না।”
গুরুপদর মাথা ঘুরতে লাগল। চোখের সামনে মশার মতন পোকা উড়তে লাগল নেচে নেচে। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। কোনো রকমে বললেন, “আমি আর বাঁচব না?”
“বাঁচার পথ কি খোলা রেখেছ যে বাঁচবে!”
গুরুপদ শুকনো গলায় বললেন, “তুমি ভাই আমাকে আর ভয় দেখিয়ো না। এমনিতেই আমি মরছি। বন্ধু লোক তুমি, ডাক্তার মানুষ। তুমি কিছু করো।”
সুবোধ বললেন, “আমি যন্ত্র। যন্ত্রী তো তিনি—” বলে ডাক্তার ছাদের দিকে আঙুল দেখালেন। “ওপরঅলাই হিসেবের খাতা ঠিক করে রেখেছেন। তাঁর হিসেবে যা আছে তাই হবে।—যাক গে, কাগজগুলো রেখে যাও। কাল পরশু একটি বার এসো। দেখি কী করা যায়। একটু ভেবে নিই।”
গুরুপদর তর সইছিল না। বললেন, “দেরি করে কী লাভ?”
সুবোধ ধমক মেরে বললেন, “বাহান্নটা বছর দেরি করলে আর এখন দু রাত্তির তোমার কাছে বেশি হল। যাও, মিথ্যে বকিয়ো না। বাড়ি যাও। লেট মি থিংক। পরশু সন্ধেবেলায় চলে এসো।”
“তুমিও তো বাড়িতে আসতে পারো! গিন্নি বড় চিন্তায় থাকবে। তুমি গিয়ে বুঝিয়ে বললে ভাল হয়—!”
সুবোধ ডাক্তার রাজি হয়ে গেলেন। পরশু মানে রবিবার।
রবিবার সন্ধেবেলায় সুবোধ ডাক্তারের চেম্বার বন্ধ থাকে।
গুরুপদ উঠতে যাচ্ছিলেন, সুবোধ হঠাৎ বললেন, “তোমার গিন্নির চেক আপটাও করিয়ে নিলে পারতে, গুরুপদ! এক যাত্রায় পৃথক ফল হয়ে লাভ কিসের?”
“কথাটা মন্দ বলোনি হে! গিন্নিরও শরীর ভাল যায় না। তা তুমি যখন বাড়িতে যাবে, বুঝিয়ে বোলো একবার। আজ আসি ভাই।”
“এসো।”
চেম্বারের বাইরে এসে গুরুপদ দেখলেন, তাঁর গাড়ি রাস্তার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে আছে। কাছাকাছি একটা সিনেমা হাউস, পাড়াটাও বাজারপাড়া। ফলে রিকশা, অটো, মিনিবাস, বাসে রাস্তার যা অবস্থা তাতে এপার থেকে ওপারে যেতে হলে গাড়ি চাপা পড়ার ষোলো আনা আশঙ্কা।
এই ভরসন্ধেতে গাড়িচাপা পড়ে মরতে রাজি নন তিনি। হাত নেড়ে চেঁচিয়ে ড্রাইভারকে ডাকতে গিয়ে দেখলেন, ভিড়ভাড়াক্কা হইহল্লার মধ্যে তাঁর গলা দশ পনেরো হাত দূরেও পৌঁছচ্ছে না। গাড়িও বার বার আড়াল পড়ে যাচ্ছে।
গুরুপদ রাস্তার একটি ছেলেকে বললেন, “বাবা, ওই যে নীল গাড়িটা, ওর ড্রাইভারকে একটু বলবে, গাড়ি ঘুরিয়ে এদিকে আনতে।”
ছোকরা গুরুপদকে দেখল। তারপর বলল, “দাদু, এই রাস্তায় এখন গাড়ি ঘুরবে না। জাম্প লেগে যাবে। দশটা টাকা ছাড়ন—দুজনকে ডেকে আনি, আপনাকে ঠেলে দেব। ভিড়ে যাবেন।”
গুরুপদ একেবারে থ। কী ছেলে রে বাবা! বলতে যাচ্ছিলেন, “বাঁদর, জন্তু কোথাকার!” বললেন না। একে বেপাড়া, তায় লক্কা ছোঁড়া। মনে মনে বললেন, “শালা!”
ছোকরা একগাল হেসে চোখ টিপে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, “বুড়ো দোতলা বাস মাইরি।”
গুরুপদ কথাটা কানে শুনলেন। কিছুই বলতে পারলেন না।
বাড়ি এসে গুরুপদ নিজের শোবার ঘরে ঢুকে পাখা খুলে দিলেন। আলো জ্বলছিল ঘরে। পা পা করে দোতলায় উঠেও হাঁফ লাগছিল তাঁর।
এমন সময় শশিতারার উদয় হল। ঘরে ঢুকে স্বামীকে বললেন, “গিয়েছিলে?”
গুরুপদ কোনো জবাব দিলেন না। এমন মুখ করে বসে থাকলেন যেন জগৎ সংসার অসার হয়ে গিয়েছে তাঁর কাছে।
“হল কী তোমার?”
গুরুপদ বললেন, “শশি, আমি আর বাঁচব না।” বলে বিরাট করে নিঃশ্বাস ফেললেন।
“কী? বাঁচবে না?”
“ডাক্তার বলল, সামনে শমন—”
“শমন?”
“ওই মরণ আর কি!”
“কার, তোমার না তার।” শশিতারার গলা রুক্ষ হয়ে উঠল।
গুরুপদ বললেন, “আমার! ডাক্তার বলল, আমার সব খারাপ হয়ে গিয়েছে। পাঁচটা—কি বলে পাঁচটা ইন্দ্রিয়।”
শশিতারা মাথায় কাপড় দেন না। সে বয়েস আর নেই। দেহের যা বহর তাতে এগারো হাত শাড়িও টেনেটুনে পরতে হয়, মাথায় কাপড় তোলার উপায় থাকে না, দরকারই বা কিসের।
শশিতারা ঝাঁঝিয়ে উঠে বললেন, “চুলোয় যাক ইন্দ্রিয়। কবেই বা ভাল ছিল! …বাজে কথা থাক—। আসল কথা বলো। তোমার ডাক্তার কী বলল?”
“বললাম তো! আমার সব খারাপ হয়ে গিয়েছে। বরবাদ হয়ে গেছে। শরীরে কিছু নেই।” বলতে বলতে ইশারা করে জল চাইলেন গুরুপদ।
শশিতারার ঘরেই জল ছিল। ঠাণ্ডা জল। জল গড়িয়ে এনে স্বামীকে দিলেন।
জল খেয়ে বড় করে নিশ্বাস ফেললেন গুরুপদ। তারপর বললেন, “সুবোধ পরশু বাড়িতে আসবে।”
শশিতারা বিরক্ত হয়ে বললেন, “আসবে আসুক। আমি জানতে চাইছি—অত যে রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন হল—তো সেসব দেখে তোমার বন্ধু বললটা কী? কিসের ব্যারাম?”
গুরুপদ একটু থিতিয়ে গিয়েছিলেন। গায়ের জামাটা খুলতে খুলতে এবার বললেন, “বলল, প্রেশার সুগার হার্ট—সবই খাবি খাচ্ছে। যে কোনো সময়ে ফট হয়ে যেতে পারি!”
শশিতারার ঠোঁট মোটা। মানুষটিও গায়ে গতরে স্বামীর সমান। একশো কেজির ধারে কাছে। গায়ের রঙের অমিল না থাকলে, এবং খানিকটা মুখের ছাঁদের—স্বামীস্ত্রীকে যমজ বলে চালিয়ে দেওয়া যেত।
শশিতারা ঠোঁট উলটে বললেন, “ফট—! তোমার সুবোধ ডাক্তার ফট বললেই ফট? সে ভগবান নাকি! যা মুখে এল বললাম আর তুমিও তার বাক্যি বলে মেনে নিলে! ও আবার ডাক্তার নাকি? কম্পাউন্ডার!
“কম্পাউণ্ডার?”
“তা নয়তো কি! আমি ওকে হাড়ে হাড়ে চিনি। সাত বার ফেল করে পাস করেছে।”
গুরুপদ একটু যেন খুশি হলেন। সুবোধ তাঁকে বড় দমিয়ে দিয়েছে। শশিতারার কাছ থেকে যেন সাহস পাওয়া গেল সামান্য। কিন্তু বন্ধুকে যেভাবে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলেন শশিতারা, তাতে আঁতে লাগল গুরুপদর। সাত সাতবার ফেল করা ছেলে সুবোধ নয়। গুরুপদ জানেন। পুরনো বন্ধুত্ব।
গুরুপদ বললেন, “সুবোধ একটা সোনার মেডেল পেয়েছিল!”
শশিতারা নাক বেঁকিয়ে জবাব দিলেন, “এ-ক-টা!—আমার বাবার একমুঠো মেডেল ছিল। সোনা রুপো—!”
“তুমি সুবোধকে ফেলনা ভেবো না, শশি! এত বছর প্র্যাকটিস করছে। জমজমা প্র্যাকটিস। কী ভিড়ও রোগীর! পয়সাও মন্দ করেনি।”
“পাড়ার মদন মুদিও পয়সা করে কদমঘাটায় বাড়ি করেছে। তাতে হয়েছেটা কী!” শশিতারা বললেন, “যাক—তোমার সুবোধকে নিয়ে তুমি থাকো। আমি তার একটা কথাও বিশ্বাস করি না। তোমার অসুখটা কী আমার জানা দরকার। হেঁয়ালি ধোঁয়ালি শুনে লাভ নেই আমার।”
গুরুপদ বললেন, “পরশু ও আসবে। জিজ্ঞেস কোরো।” বলেই তাঁর অন্য কথা মনে পড়ে গেল। আবার বললেন, “সুবোধ বলছিল, তোমারও একবার চেক আপ করানো দরকার।”
শশিতারা হাত উঠিয়ে ঝাপটা মারার ভঙ্গি করলেন, “থাক, আমার আপ-টাপে দরকার নেই। বেশ আছি। তুমি নিজেরটা দেখো। নাও, ওঠো, গা ধুয়ে এসো, ফল শরবত খাও।”
শশিতারা আর দাঁড়ালেন না।
গা-হাত ধুয়ে গুরুপদ ঘরে বসলেন। পরনে সাদা লুঙি, গায়ে বগলকাটা পাতলা ফতুয়া। পায়ে মোটা হাওয়াই চটি।
আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়ে নিলেন। অল্প চুল। হু হু করে পেকে যাচ্ছে।
নিজের মুখের চেহারাটাও আয়নায় দেখলেন গুরুপদ। শশিতারা যাই বলুক, গুরুপদ নিজেই বুঝতে পারছেন, তাঁর শরীরের অবস্থা ভাল নয়। মুখটা কেমন থমথমে হয়ে রয়েছে। চোখ অল্প লালচে। নেশা ধরলে যেমন দেখায়। প্রেশারের জন্যে নাকি! কিসের যে দুর্বলতা ক্লান্তি—কে জানে! বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না। ওজন কমারও কোনো লক্ষণ নেই। রোজ সকালে বাড়ির ছাদে পাক মারছেন, ফুলের টবে জল ঢালছেন—তবু ওজনের কমতি হচ্ছে না। ভুঁড়িরও হ্রাসবৃদ্ধি নেই। সেই একই রকম।
মনের দুশ্চিন্তাই বড় শত্রু। গুরুপদর সময়টা ভাল যাচ্ছে না। বছরখানেক ধরে নানা গণ্ডগোলের মধ্যে রয়েছেন। কারখানায় একটা না একটা ঝামেলা লেগেই আছে। আজ ষোলো দফা দাবি, কাল হুমকি, পরশু ঘেরাও। পাগলা হয়ে যাবার জোগাড়। আরে বাবা, তোরা তো বোকা কালিদাসকেও হার মানালি। কালিদাস নিজে যে ডালে বসেছিল সেই ডাল কাটছিল। তোরা এমন মুখ্যু—ডালপালা তো তুচ্ছ, গোটা গাছটাই উপড়ে ফেলার জন্যে লেগে পড়েছিলি। তাতে গুরুপদর আর কী হত, কারখানা বন্ধ হয়ে যেত, মাস কয়েক পরে দেখতিস লছমনদাস বাজপুরিয়া কারখানা কিনে নিয়েছে, নিয়ে নতুন নাম দিয়ে কারখানা চালু করেছে। গুরুপদ ঠকত না, ঠকতিস তোরা। বাঙালির এই হল দোষ; চরিত্তির। নিজের মুখের রুটি হাতে নিয়ে খেলা করে; আর চিল এসে ছোঁ মেরে নিয়ে চলে যায়।
গুরুপদ তেমন একবগ্গা মালিক নন। কত রকমভাবে বুঝিয়েছেন, মিষ্টি করে কথা বলেছেন, মাইনেপত্র বাড়িয়েও দিয়েছেন, মায় মাসে পনেরো টাকা করে টিফিন খরচাও ধরে দিয়েছেন রফা করে। তবু মন তুষ্ট করা যায় না। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচির মতন তাঁর কারখানা ছোট—লোক বিস্তর।
শেষে একদিন গুরুপদ বললেন, “নরম মাটি পেয়ে আমায় তোমরা পায়ে চটকাবে? হবে না। আমি আর কারখানায় আসব না; কথাও বলব না। যা খুশি করো তোমরা।”
তেরিয়া না হলে আজকালকার সংসারে কাজ হয় না। গ্রাহ্যি করে না লোকে। গুরুপদর উকিল নীলমণি চাটুজ্যে ঠিকই বলে। বলে, কলকাতা শহরে মানুষ মিনিবাসকে ডরায় কেন গুরুপদবাবু? অ্যাজ বিকজ দে আর অল ডেসপারেটাস। নীলমণি ইংরিজি শব্দের শেষে নাকি ইটালি ভাষা মেশাতে পছন্দ করে।
গুরুপদ কি আর মিনিবাস? মানুষ বলে কথা। আর ব্যবসা তো, আমলা তেল, চালমুগরার সাবান, শাঁখের গুঁড়ো উইথ চন্দন—এ সবের। আর হালে তৈরি করেছিলেন কাপড়কাচা গোল সাবান। দেখতে গেলে কিছুই নয়। তবে ভাল ভাল নাম দিয়েছিলেন জিনিসগুলোর। ‘আদি আমলা শশি কেশ তৈল’ ‘চর্মদশানন চালমুগরা’ ‘মুখশোভা; শঙ্খ চন্দন চূর্ণ’। কাপড়কাচা গোল সাবানের নাম; ‘নব বাংলা সাবান’।
গুরুপদ ব্যবসার মূল কথাটা জানেন; পাবলিকের যা হামেশাই দরকারে লাগে তা নিয়ে ব্যবসা করো, যত তুচ্ছ জিনিসের হোক, লেগে যাবে। পাড়ায় পাড়ায় মুদির দোকান কেন চলে? কেন পানের দোকান ফেল মারে না? তেলেভাজার দোকানে গিয়ে লাইন মারতে হয় কেন?
পঁচিশ বছর আগে গুরুপদ যখন নিতান্তই চাকরি করতেন একটা ফারমাসিউটিক্যাল কম্পানিতে তখন থেকেই মাথায় ব্যবসার পোকা নড়েছিল। বিয়ের পর এক মামা-শ্বশুরের দর্শন পেলেন। গুরুদর্শন। মামাশ্বশুর আলপিন, সেফটিপিন, ক্লিপ তৈরি করে চারতলা বাড়ি হাঁকিয়েছেন। পাতিপুকুরে মামাশ্বশুরমশাই বললেন, খোস-পাঁচড়া-দাদের মলমের কত বিক্রি জানো, বাবাজি। এ দেশ হল গরিবের দেশ; এখানে যত লোক পাউডার মাখে তার পাঁচশ গুণ লোক দাদ চুলকুনি হাজার ওষুধ খুঁজে বেড়ায় বুঝলে? রাইট জিনিস পিক করো, লেগে যাবে।
গুরুপদ পাঁচ রকম ভেবেচিন্তে প্রথমেই ধরলেন, ‘আদি আমলা শশি কেশ তৈল’। বন্ধুরা বলল, ‘আমলার আবার আদি কী রে? গুরুপদ হেসে বললেন, ‘আদির একটা মার্কেট ভ্যালু আছে। আদি কবি বাল্মীকি, ব্রাহ্ম সমাজ, আদি ঢাকেশ্বরী—পুরনো ঘিয়ের গন্ধ ভাই। আর শশি আমার লাক—দেখা যাক বাজারে লাগে কিনা!”
কাগজে পাঁজিতে বিজ্ঞাপন। শিয়ালদা হাওড়া স্টেশনে হ্যান্ডবিল। আমলা তেল বাজারে লেগে গেল। বাজারে মানে বাবুবিবিদের বাজারে নয়, ছাপোষা গরিব-গুর্বোদের ঘরে। মফস্বলে মার্কেট হয়ে গেল। আমলার সাফল্যে খুশি হয়ে গুরুপদ ‘চর্মদশানন চালমুগরায়’ নেমে গেলেন। পাঁজিতে পাতাজোড়া বিজ্ঞাপন। বিবিধভারতীতে স্পট। চমর্দশাননও সাকসেস। তারপর মুখশোভা শঙ্খ চন্দন চূর্ণ।
সাত আট বছরের মধ্যে গুরুপদ পায়ের তলায় শক্ত মাটি পেয়ে গেলেন। শোভাবাজারের দিকে একটা ভাঙা পোড়া বাড়ির নীচের তলার একপাশে তাঁর ‘শশিতারা কোং’ চলতে লাগল। চলতে চলতে পুরো নীচের তলাটাই তাঁর কারখানা হয়ে গেল। জনা তিরিশ লোক খাটে কারখানায়।
গুরুপদ টাকার স্বাদ বোঝার পর থেকেই মন প্রাণ ঢেলে দিলেন ব্যবসায়। আজ বিশ বছরে তিনি না করলেন কী! পাইকপাড়ায় তেতলা বাড়ি করেছেন। কারখানার জন্যে একটা ভ্যান রয়েছে। মধ্যমগ্রামের দিকে বাগান কিনে ফেলে রেখেছেন।
ভাগ্য একদিকে গুরুপদকে যথেষ্ট দিয়েছে। অন্যদিকে অবশ্য মেরে রেখেছে। গুরুপদরা সন্তানহীন।
বছর সাত আট অপেক্ষা করার পরও যখন শশিতারার কিছু হল না, ডাক্তার বদ্যি, তাবিজ মাদুলি, পাথর, মায় উত্তরপাড়ার ডাকসাইটে তান্ত্রিক গুরুর যাগযজ্ঞ পর্যন্ত বিফলে গেল—তখন শশিতারা বললেন, দত্তক নেবেন। গুরুপদ আপত্তি করলেন না। করে কী লাভ? স্ত্রী থেকেই তাঁর ভাগ্যে শশির উদয়। স্ত্রীকে ভয়ভক্তি করেন গুরুপদ। ভালও বাসেন।
শশিতারা তাঁর এক সম্পর্কের বিধবা বোনের ছেলেকে হাফ দত্তক নিলেন। মানে লালনপালনের সব দায়দায়িত্ব। কিন্তু আইনগতভাবে নয়। সে বোনও বিগত হল।
গুরুপদর একটা মেয়ে মেয়ে শখ ছিল। বছর কয়েক পরে গুরুপদর ইচ্ছে হল, এক ভাগ্নিকে নিজের কাছে এনে রাখেন। না, দত্তক নয়। গুরুপদর কোষ্ঠীতে নিষেধ বলছে। বিষ্টপুর থেকে ভাগ্নিকে তুলে এনে নিজের ঘরে আশ্রয় দিলেন গুরুপদ। সেই ভাগ্নির বয়েস এখন কুড়ি। নাম, বেলা।
দত্তকরূপী ছেলের নাম ছিল চাঁদু। নাম পালটে শশিতারা তাকে সুশান্ত করে দিয়েছেন। ডাকেন, শানু বলে।
ছেলে একেবারে তৈরি। বছর বাইশ তেইশ বয়েস বড়জোর। এখনই দোল দুর্গোৎসবে দু এক পাত্র টানতে শুরু করে দিয়েছে। দিনে দু তিন প্যাকেট সিগারেট ওড়ায়।
গুরুপদ কিছু বলতে পারেন না। বললেই শশিতারা খরখর করে ওঠেন। ছেলে আমার বলে তোমার চোখ টানছে। আর নিজের মেয়ের বেলায়? তাঁর তো সাবান শ্যাম্পু চুল ছাঁটা গানের ক্লাস ছাড়া করার কিছু দেখি না। নিজের বেলায় চোখ বুজে থাকো, তাই না?
তা বেলার বেলায় গুরুপদ যতটা স্নেহান্ধ, শানুর বেলায় ততটা নয়। আর শশিতারা শানুর বেলায় যতটা লাগামছাড়া বেলার বেলায় ততটা নয়। তবে, একথা স্বীকার করতেই হবে, ছেলে মেয়ে দুটো এমনিতে খারাপ নয়; বয়েসের টানে খানিকটা তরল, চঞ্চল চপল; টাকাপয়সার সাফল্যে কিছুটা বেহিসেবি, বিলাসী। কী আর করা যাবে? গুরুপদ আর শশিতারার টাকা খাবে কে? ওদের জন্যেই সব।
গুরুপদ বিছানায় গিয়ে বসবেন ভাবছিলেন এমন সময় শশিতারা নিজের হাতে ফল আর শরবত নিয়ে ঘরে এলেন।
জানলার কাছে শ্বেতপাথরিয় চৌকো ছোট টেবিল। ফল-শরবত নামিয়ে রেখে শশিতারা বললেন, “নাও, খেয়ে নাও।”
গুরুপদ চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললেন, “খাব?”
“কেন! খাবে না কেন?”
“বুঝতে পারছি না। ব্লাড সুগার যদি আরও চাগিয়ে যায়।”
“নিকুচি করেছে তোমার ব্লাড সুগারের। রোগের কথা ভাবতে ভাবতে যা ছিরি করেছ! আগে তোমার বন্ধু আসুক। বলুক, কী হয়েছে। তারপর দেখা যাবে, কী খাবে কী খাবে না।”
গুরুপদ ফলের প্লেটে হাত দিলেন। শশার কুচি, কলা, কমলালেবু, বিশ পঁচিশটা আঙুর।
খেতে খেতে গুরুপদ বললেন, “শরীরকে আর অবহেলা করা উচিত নয়, শশি। প্রেশার সুগার—দুটোই খুব খারাপ। তার ওপর হার্ট। সুগারে লোকে নাকি অন্ধ হয়ে যায়।”
শশিতারা বললেন, “কে বলেছে তুমি অন্ধ হবে! তোমার ওই সুবোধ?”
“না না, সে বলেনি। আমি শুনেছি।”
“শোনা কথার আবার কী দাম গো?”
একটু চুপ করে থেকে গুরুপদ বললেন, “আজকাল বুকের ভেতরটাও কেমন করে। চাপ চাপ লাগে। ব্রিদিং ট্রাবল…”
“ওসব তোমার বাই। ⋯আমারও তো মনে হয়, বুক না বালির বস্তা। নোয়াতে পারি না।”
গুরুপদ স্ত্রীর বুকের দিকে তাকালেন। ওই বুকের আর নোয়ানোর কিছু নেই। পেট বুক এক। শশিতারাকে এখন দেখলে কে বিশ্বাস করবে, বিয়ের সময় শশির ওজন ছিল মাত্র তিরিশ সের। এক কি দু কলা উদয় ঘটেছিল শশির। চমৎকার ছিপছিপে গড়ন ছিল তার। তবে মাথায় খাটো। গুরুপদ নিজেও মাথায় লম্বা নন। বরং বেঁটেই বলা যায়। বিয়ের সময় জোড় মন্দ মানায়নি। এখন অবশ্য জোড় হিসেবে মানানসই হয়ে আছেন। পাড়ার লোক আড়ালে বলে জোড়া গিরজে।
শশিতারা হঠাৎ বললেন, “রোগের কথা রাখো। তোমায় একটা খবর দি। রসময় এসেছিল আজ বিকেলে। বড় ঝোলাঝুলি করছে।”
গুরুপদ স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকলেন। এমন সময় পাশের ঘরে ফোন বেজে উঠল।
শশিতারা উঠে গিয়েছিলেন ফোন ধরতে। ফিরে আসতে সামান্য সময় লাগল।
ফিরে এসে বললেন, “তুমি চশমা ফেলে এসেছ ডাক্তারের ঘরে?”
গুরুপদর খেয়াল হল। কাছের জিনিস দেখতে, কাগজটাগজ পড়তে তাঁর চশমা লাগে। সুবোধের চেম্বারে চশমাটা পকেট থেকে বার করেছিলেন। আসার সময় মনের যা অবস্থা হয়েছিল চশমাটা খাপে ভরতে ভুলে যেতেই পারেন।
গুরুপদ বললেন, “কী জানি! আমার পকেটটা দেখো একবার।’
শশিতারা এগিয়ে গিয়ে স্বামীর ছেড়ে রাখা পাঞ্জাবিটা ঘাঁটলেন। না চশমার খাপ নেই। বললেন, “কাল সকালে দিনুকে পাঠিয়ে দেব। চশমাটা নিয়ে আসবে।’
চশমার জন্যে গুরুপদর ব্যাকুলতা দেখা গেল না। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, “সুবোধের সঙ্গে তোমার কথা হল?”
“হল।” শশিতারা ফিরে এসে স্বামীর কাছাকাছি বসলেন।
“কী বলল?”
“ছ্যাচড়ামি করল” শশিতারা যেন খানিকটা বিরক্ত। বললেন, “সামনাসামনি হলে দেখে নিতুম। ফোনে তো অত কথা বলা যায় না।”
“বলল কী?”
“ঠুকে ঠুকে কথা বলল; রসিকর্তা করল। বলল, কর্তাকে খাঁটি গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচি, পোলাও, মাংস, পাকা রুই মাছের পেটি, দুধ, সন্দেশ, রাজভোগ খাইয়ে যাও⋯, বলি চোখ আছে না নেই, তার যে চেহারাখানা তৈরি করেছ, এমন চেহারা অর্ডার দিয়ে কুমোরটুলিতেও গড়ানো যায় না। —বেলুন ফোলাতে ফোলাতে কোথায় নিয়ে গেছ—তোমার চোখেও পড়েনি। পতিভক্তি যা দেখালে—এবার তার ঠেলা বুঝতে হবে।”
“বলল তোমায়?”
“বলল। আরও কত রকম রসিকর্তা।—আমিও ছেড়ে কথা বলার লোক নই।”
“তুমিও বললে?”
“বলব না।—আমিও বললুম, যার পুকুর তার মাছ, অন্য লোকের বুকে বাজ। নিজেরটি তো হারিয়েছ তাই অন্যেরটি দেখে আফসোসে মরো। বেশ করেছি আমি আমার কর্তাকে গাওয়া ঘিয়ের লুচি-মাংস খাইয়েছি। তোমার বউ বেঁচে থাকতে কোনদিকে ঘাটতি ছিল তোমার। তখন নিজে যে কুমারটুলির কার্তিক হয়ে ঘুরে বেড়াতে। আমাকে বাজে বকিয়ো না। তোমার মতন ডাক্তার আমি ট্যাঁকে গুঁজতে পারি।”
গুরুপদ ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, “সুবোধকে তুমি এসব বললে?”
“কেন বলব না! আমার পেছনে লাগতে এলে আমি ছেড়ে দেব!”
“না না, তা নয়। তবে কিনা কতকালের পুরনো বন্ধু, ভাল ডাক্তার। তা ছাড়া তোমাদেরও নিজের লোকের মতন ছিল। যদি কিছু মনে করে!”
“করলে করবে। আমায় যখন যা-তা বলে তখন কি তোয়াক্কা করে মুখের।”
গুরুপদ আর ও পথে গেলেন না। শুধু বললেন, “পরশু আসবে তো?”
“আসবে।”
কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর গুরুপদ বললেন, “রসময়ের কথা কী বলছিলে?”
শশিতারার পান-জরদার নেশা। পানের কৌটো আনতে ভুলে গিয়েছিলেন। আবার উঠলেন। দরজার কাছে গিয়ে হাঁক মারলেন, “পারুলের মা—আমার পানের ডিবেটা দিয়ে যাও।”
পানের ডিবে, জরদার কৌটো আসতে সময় লাগল। দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকলেন শশিতারা।
পারুলের মা পানের ডিবে দিয়ে চলে যাচ্ছিল, শশিতারা বললেন, “দাদা-দিদি ফেরেনি এখনও?”
“এই ফিরল।”
“ঠিক আছে।”
শশিতারা আবার স্বামীর কাছাকাছি এসে বসলেন। পান জরদা মুখে দিয়ে বললেন, “রসময় বলছিল, ও পক্ষ বড় তাড়া দিচ্ছে।”
“কোন পক্ষ?”
“কোন পক্ষ আবার! ছেলেদের তরফে তাড়া দিচ্ছে।”
গুরুপদর খেয়াল বল। বললেন, “আমি তো বলেই দিয়েছি, বেলুর বিয়ে এখন আমি দেব না।”
শশিতারা বললেন, “কেন?”
“কেন আবার কী! উনিশ কুড়ি বছর বয়েসে—এখন বিয়ে?”
শশিতারা স্বামীকে লক্ষ করলেন। বিরক্ত হয়ে বললেন, “উনিশ বছরে মেয়েদের বিয়ে হয় না? আমার কত বছর বয়েসে বিয়ে হয়ে ছিল। উনিশ কুড়ি।”
“সে তখন। এখন কুড়ি একুশ কম করে। চব্বিশ পঁচিশের আগে মেয়েরাও বিয়ে করে না।”
“ও ! তোমার মতলব তা হলে এখনও দু চার বছর তোমার বেলুকে গলায় ঝুলিয়ে রাখা।”
গুরুপদর হাই উঠল। বড় করে হাই তুলে মুখের সামনে তুড়ি মারলেন। পরে বললেন, “এত হইচইয়ের আছে কী। সময়ে বিয়ে হবে।”
“হ্যাঁ, হবে। ততদিন এই ছেলে বসে থাকবে নাকি! নিজের জায়গায় ফিরে যাবে। সাত সুমুদ্র উড়ে তোমার মেয়েকে বিয়ে করতে আসবে না।”
গুরুপদ নির্বিকার গলায় বললেন, “দরকার নেই আসার।”
শশিতারা চটে গেলেন। গুরুপদ এমনভাবে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে পাত্র তাড়াচ্ছেন, যেন অমন পাত্র শয়ে শয়ে দেখা যায়। কাক বককে মানুষ এই ভাবে তাড়ায়। রেগে গিয়ে শশিতারা বললেন, “আমেরিকায় থাকে ছেলে, দিদি ভগিনীপতির সঙ্গে। ভাল চাকরি-বাকরি করে দেখতে ভাল। টাকাপয়সার অভাব নেই। মেয়ে তোমার সুখে থাকত। নিজেরা যেচে হাত বাড়িয়েছিল। তুমি হাতের জিনিস পায়ে ঠেলছ।”
গুরুপদ বললেন, “আমেরিকা, লন্ডন আমার দরকার নেই। আমলা তেল আর চালমুগৱো সাবানের ব্যবসা করি আমি। একবারে দেশি ছেলের সঙ্গে বেলুর বিয়ে দেব।”
সেই ছেলে কি তোমার গোকুলে বাড়ছে?”
“কপালে বাড়ছে। কে কার জন্যে বাড়ে তুমি জান? আমি কার জন্যে বেড়েছিলাম।”
শশিতারা বললেন, “ঠিক আছে। থাক তোমার মেয়ে ধিঙি হয়ে ওই তো কাঠবেড়ালি চেহারা। দেখি কোন গোকুল এসে নিয়ে যায়!”
দুই
শানু আর বেলার ঘর পাশাপাশি। দোতলায় বারান্দার দিকের দরজা ছাড়াও দু ঘরের মাঝামাঝি দরজা আছে। খোলাই পড়ে থাকে। সারাদিন। রাত্রে শোবার সময় দরজাটা বন্ধ করে দেয় বেলা। কোনোদিন বা শুধু ভেজিয়ে রাখে। বেলার ছেলেবেলা থেকেই ভূতের ভয়। সে যখন বিষ্ণুপুরে ছিল তখন তাদের বাড়ির পাঁচ সাতটা বাড়ি তফাতে রাধার মাকে ভূতে ধরেছিল। বটগাছের মাথা থেকে নেমে সেই যে ভূতে ধরল মাকে—একটানা পাঁচ ছ মাস বেচারিকে নাস্তানাবুদ করে যখন ছেড়ে দিল তখন বাতাসিমাসি—মানে রাধার মায়ের হাড়চর্মসার চেহারা। বাতাসিমাসি মারাও গেল পরে।।
ছেলেবেলায় স্বচক্ষে বেলা ভূতে ধরার ব্যাপারটা দেখেছে। আহা, বাতাসিমাসি না পারত খেতে, না পারত শুতে। কুয়োতলায় রান্নাঘরে, উঠোনে, কলঘরে দুমদুম করে আছাড় খেত, মুখ দিয়ে গেঁজলা বেরত, আবোতল তাবোল বকত, কখনও কাঁদত, কখনও গালগাল দিয়ে খারাপ খারাপ কথা বলত। আরও কত কী করত।
বেলার তখন থেকে ভূতের ভয়। ভয় আর কাটল না।।
একা ঘরে শুতে বেলার আপত্তি নেই। তার ঘর। নিজের মতন করে সে সাজিয়ে গুছিয়ে গা হাত ছড়িয়ে মহা আরামে থাকে। ঘরের লাগোয়া বাথরুম। ছিটেফোঁটাও অসুবিধে নেই। তবু—ওই যে—কোনোদিন যদি কোনো কারণে একবার গা শিউরে ওঠে, বেলা হয়ে গেল। শানু আর তার ঘরের মাঝখানের দরজা সে আর বন্ধ করবে না, আলগাভাবে ভেজিয়ে রাখবে শোবার আগে।
শানুও এক একদিন মজা করে। কোথাও কিছু নেই, বেলা হয়তো সন্ধেবেলায় বসে বসে কলেজের পড়া দেখছে, শানু কোথা থেকে একটা গোবদা বই এনে বেলার কাছে ফেলে দিল। “বেলা দারুণ দারুণ ভূতের গল্প আছে বইটায়। পড়ে দেখ। গায়ে কাঁটা দেবে।” কখনও বা “মৃত্যুর পরপারে” “প্রেতসিদ্ধ মহারাজ নকুলেশ্বর” “কলকাতা শহরের ভূতের বাড়ি”—এই ধরনের বই বা লেখা এনে বেলাকে পড়ে পড়ে শোনাবে।
বেলা চেঁচাবে, ঝগড়া করবে, কাঁদবে—কিন্তু ভয়টা মন থেকে তাড়াতে পারবে না।
“আমি তোর পাশের ঘরে থাকব না, তেতলায় চলে যাব” বেলা হয়তো বলল।
“চলে যা! আমার দু-দুটো ঘর হয়ে যাবে।” শানুর জবাব।
“সবই তো তোর। ”
“অফকোর্স। আমি বাড়ির ছেলে, তুই মেয়ে। তোর বিয়ে হলেই কাটিয়ে দেওয়া হবে। তখন তোর কপালে যা আছে। তার শাশুড়ি তোকে কেরাসিন তেল ঢেলে পুড়িয়ে মারতে পারে। শ্বশুর আর তোর বর মিলে তোকে কোপাতে পারে! বেলি, পোড়া মানুষের যা চেহারা হয় দেখেছিস! বীভৎস। আর আগুনে পুড়ে, খুনখারাবি হয়ে মরলে নির্ঘাত ভূত।”
বেলা হাতের সামনে যা পেল ছুঁড়ে মারতে লাগল শানুকে। “তুই আমাকে তাড়াতে পারবি? আমি যাব না। এটা আমার মামার বাড়ি।”
“আমার মাসির বাড়ি। মায়ের বাড়িও বলতে পারিস। আমি একরকম দত্তক, তুই তক্ষক।”
বেলার মুখ অভিমানে অপমানে থমথম করে উঠত। জল আসত চোখে।
শানুকে চেষ্টা করতে হত বেলার রাগ অভিমান ক্ষোভ ধুয়ে মুছে তার মুখে হাসি ফোটাতে।
সম্পর্কটা এই রকমই ছিল। চিমটি কাটার, চটিয়ে দেবার, ভয় পাইয়ে মজা পাবার এই শানু আর বেলা পরস্পরকে হাসি তামাশা অন্তরঙ্গতার অবলম্বন করে নিয়েছিল।
সেদিন দুজনে খাওয়া শেষ করে নিজেদের ঘরে এল গম্ভীর মুখে।
ঘরে এসে বারান্দার দরজা বন্ধ করে দিয়ে শানু একটা সিগারেট ধরাল।
বেলা নিজের ঘরে।
শানু আবার ডাকল, “বেলি?”
এবার সাড়া দিল বেলা।
শানু ডাকল, “এখানে আয়।”
বেলা মাঝের দরজা দিয়ে শানুর ঘরে এল।
“কী বুঝলি?” শানু বলল।
বেলা কোনো জবাব দিল না।
শানু মুখের ধোঁয়া গিলে ফেলে বলল, “তোর মামার নাকি মহাপ্রস্থানে যাবার অবস্থা হয়েছে। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত রোগে রোগে ভরতি। প্রেশার, সুগার, হার্ট, কিডনি, লিভার—।”
বেলা বাধা দিয়ে বলল, “আমার মামা তোমার মেসো। ধর্ম বাবাও।”
“ম্যাটার লাইজ দেয়ার—। মাসি কেমন বলল শুনলি? শানু সঙ্গে সঙ্গে শশিতারার গলা নকল করে বলতে শুরু করল, “সংসারে একটা মানুষ মাথায় গন্ধমাদন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সকাল দশটায় বেরোয় রাত আটটায় বাড়ি ফেরে। যত্ত ঝক্কি ঝামেলা, টাকাপয়সা ব্যবসার চিন্তা তার। খেটে খেটে ভাবনায় ভাবনায় তার সতেরো রকম রোগ বাঁধল। ডাক্তার বলেছে, এভাবে চললে দু দিনেই ফট। চাট্টিখানি কথা নাকি। মাত্তর পঞ্চাশ বাহান্ন বয়েস হল, এখন তো চুল পাকা দাঁত পড়ার বয়েসও হয়নি। অথচ কী দশা হয়েছে মানুষটার চোখ খুলে দেখা যায় না। শরীর পাত হয়ে গেল।—আর তোমরা বাবুবিবিরা মনের আনন্দে ছররা করে বেড়াচ্ছ। তোমাদের না চোখ আছে, না চোখের পাতা আছে। কার ছায়ার তলায় দাঁড়িয়ে আছ বুঝতে পারছ না। বুঝবে একদিন। ছি ছি—!”
শানু শশিতারার পার্টে প্রক্সি দিয়ে হাতের সিগারেটটা জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিল।
বেলা বলল, “ওই কথাটা আমার খুব খারাপ লেগেছে।”
“কোন কথা?”
“ওই যে মামি বলল—যার যায় তার যায়—অন্য লোকের আয় দেয়। ”
শানু খেয়াল করে কথাটা শোনেনি। শুনলেও পরোয়া করেনি। মাসির একটু ছড়াকাটা অভ্যেস আছে। মেয়েলি ছড়ায় কে কান করে?
শানু বলল, “ছেড়ে দে। বাজে কথায় কান করিস কেন?”
বেলা বলল, “বাজে কথা! এটা বাজে কথা হল? মামার শরীর খারাপ হলে আমাদের কোন আয় বাড়বে—তুইই বল।”
শানু বলল, “ধুত, তুই এনিয়ে মাথা ঘামাতে বসলি! মুখে এসেছে বলে ফেলেছে। মাসির ওই টাইপ। মন থেকে কিছু বলে না। ভেবেও বলে না।” বলে শানু একটা চেয়ারে বসে পড়ল। মাথার চুল ঘাঁটল সামান্য। আবার বলল, “তোর কী মনে হয়?”
“কিসের?”
“মেশোর শরীর দেখে কী মনে হয় তোর?”
বেলা কী বলবে বুঝতে পারল না।
“মেসোকে সিক মনে হয়?”
বেলা একটু অন্যমনস্কভাবে বলল, চোখে দেখে কি অসুখ বোঝা যায়। ডাক্তার যখন বলছে”—
“ডাক্তাররা এইট্টি পার্সেন্ট ফালতু কথা বলে। —তোর মনে নেই, আমার হল ম্যালেরিয়া ডাক্তার বলল প্যারাটাইফয়েড। তোর হল টনসিলাইটিস—বলল, ডিপথেরিয়া। মাসির কান পাকল, বলল নাকের মধ্যে ফোঁড়া হয়েছে। যত্ত বোগাস।”
বেলা বলল, “ সে পাড়ার ডাক্তার ঘোষবাবু। সুবোধ মামা বাজে কথা বলার লোক নয়। তোর আমার বেলায় তো সুবোধ মামাই পরে এসে দেখে ঠিকঠাক বলে ওষুধপত্র দিয়ে গেল।”
শানু কথাটা অস্বীকার করতে পারল না। এবাড়িতে তেমন বেগড়বাঁই কিছু হলে সুবোধ মেসোকেই ডাকতে হয়। আসলে সুবোধ মেশোমশাই থাকেন মাঝ কলকাতায়, আর শানুরা থাকে পাইকপাড়ায়। দরকারে পাড়ার ডাক্তারকেই ডাকতে হয় প্রথমে। আর তাদের পাড়ার ঘোষ একটা ছাগল। এ গোট উইথ টু লেগস।
শানু বলল, “তুই বোস না। ব্যাপারটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হবার নয়। ভাবতে হবে। ডিপলি ভাবতে হবে। সাপোজ মেশোর দারুণ কিছু হয়েছে —বডির ফাংশন খারাপ হয়ে গিয়েছে, সিস্টেম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—তা হলে আমাদের চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। একটা কিছু করতেই হবে।”
বেলা আর দাঁড়িয়ে থাকল না, শানুর বিছানায় বসল। মনে মনে এখনও সে অখুশি। মামির ওই কথাটা তার প্রাণে ভীষণ বেজেছে। মামাকে সে কম ভালবাসে না, সেই মামার কিছু হলে তার লাভ কিসের! বেলা কি তেমন স্বার্থপর!
শানু বলল, “বেলি, আমার মনে হয় মেসোর রক্তটক্ত আর একবার পরীক্ষা করানো দরকার। ভাল জায়গা থেকে। আর একটা ই সি জি।—তুই জানিস না পাড়ার শেতলা মন্দিরের মতন রাস্তায় ঘাটে যত রক্তমূত্র কফ পরীক্ষার ঝুপড়ি গজিয়ে উঠেছে—তার নাইন্টি পার্সেন্ট হল রদ্দি। টাকা পেঁচার কল। কিস্যু দেখে না, এর পেচ্ছাপ ওর ঘাড়ে চাপায়, রামের ব্লাড শ্যামের বলে চালিয়ে দেয়। স্টুল রিপোর্ট এ টু জেড একই কিসিমের। এরা ডেনজারাস—।”
বেলা বলল “মামা ভাল জায়গা থেকে পরীক্ষা করিয়েছে। ”
“রাখ তোর ভাল জায়গা। নামেই ভাল। রিলায়েবল লোক দরকার। নিজে যে সব কিছু পরীক্ষা করবে, অন্যের হাতে ছেড়ে দেবে না।”
“মামাকে বল।”
“বলব। মাসিকে আগে বলি। আমি বলব, তুই আমার পোঁ ধরবি।”
বেলা বলল, “বল মাসিকে।”
শানু বলল, “তারপর রিপোর্টগুলো নিয়ে কলকাতার তিনজন টপ ডাক্তারের কাছে যেতে হবে। তারাই বলবে—কী হয়েছে। শেষে ভেবেচিন্তে একটা উপায় বার করতে হবে।”
বেলা বলল, “তুই সুবোধ মামাকে পাত্তা দিচ্ছিস না?”
“কে বলল দিচ্ছি না! সুবোধ মেসোই টপ ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলবে।”
“যা খুশি কর তুই।”
“আমি মাসিকে ম্যানেজ করব তুই মেসোকে কর।”
বেলা এবার হাই তুলল। হাই তোলার সময় হাত ছড়িয়ে গা ভাঙল।
“তোকে ফ্রাংকলি বলছি বেলি আমার কিন্তু মনে হয়—মেসোর র্যাশান কাট করলেই ভদ্রলোক ঠিক হয়ে যাবেন।”
বেলা এ ব্যাপারে আপত্তি করল না। মামি যে মামাকে বেশি খাওয়ায়—এটা সে বরাবরই দেখে আসছে। আগে অত বুঝত না, এখন বোঝে।
“বডি তো বেলুন নয় যে যত্ত খুশি ফুলিয়ে যাও। বেলুনও ফটাস হয়ে যায়,” শানু বলল, “মাসি সকাল থেকে যা শুরু করে। চার বেলা ওই রকম পেটে পড়লে তুই আমি মরে যেতাম! ডিম, ছানা, হরি মোদকের রসগোল্লা, সন্দেশ, তিন চার পিস করে একশো গ্রাম ওজনের মাছের পিস, দুধ, দই, ফল, রাত্রে লুচি ফাউল—হোয়াট নট? খাবার একটা বয়েস থাকে মানুষের। চল্লিশের পর ডায়েটিং-এ চলে যেতে হয়। সেদিন একটা কাগজে পড়ছিলাম চল্লিশের পর সারা দিনে দু টুকরো রুটি, চার চামচে মধু, এক লিটার দুধ, দু পিস মাংস, বা একটা ডিম আর সাফিসিয়ান্ট ওয়াটার খেলে মানুষের আয়ু আশি পর্যন্ত রিচ করতে পারে।”
বেলা বলল, “কিছু না খেলে একশো। ”
শানু বেলাকে দেখল। “ইয়ার্কি মারছিস।—বেলি, কিছু শিখলি না। জীবনে তোর অনেক দুঃখ। শুধু সাজতে, গান গাইতে আর কলেজে গিয়ে আড্ডা মারতে শিখলে কিছু হয় না।”
“তুই কী শিখলি? শেখার মতন তো দেখলাম, কতকগুলো চ্যাংড়া বন্ধুর সঙ্গে নীচের হলে টেবিল টেনিস খেলছিস, না হয় পপ গান শুনছিস। আর বাইরে গিয়ে সিনেমা, খেলার মাঠ, কফি হাউস করে বেড়াচ্ছিস। সিগারেট ফুঁকছিস বিশ পঁচিশটা করে পড়াশোনায় তোরও যা মাথা—!”
শানু একটু হাসল। বলল, “তুই আগাপাশতলা মুখ্যু। তোকে বললেও বুঝবি না ওরে বেলি, আমার ধর্মবাবা—মানে তোর মামা—আমলা, চালমুগরা, শাঁখ চন্দনের ভেজাল প্রোডাক্ট আর ওই বাংলা সাবান, যা রেখে যাবে তাতে আমার দু দুটো লাইফ কেটে যাবে। হোয়াই শুড আই বদার ফর এ থার্ড ক্লাস এম এস সি ডিগ্রি!—আমার চোখ-মুখ দেখ। গৌতম বুদ্ধ। বডি দেখ, চাবুক।—তোর নিজের চেহারার সঙ্গে মিলিয়ে নে।”
বেলা উঠে দাঁড়াল। বলল, “আমার সঙ্গে তুলনা করতে যাস না। আমি ফিন ফিন করছি। তোর মতন ভোঁদামাকা নয়।”
শানু বলল হাততালি দিয়ে, “ওরে আমার ফিনফিনে ফিঙে। দেখিস ফিন ফিন করতে গিয়ে ফিনিশ না হয়ে যাস।”
বেলা তার ঘরের দিকে পা বাড়াল। “নিজের চরকায় তেল দে।”
শানু হেসে বলল, “দিয়ে যাচ্ছি, ভাবিস না।— কিন্তু একটা কথা তুই জেনে রাখবি; বেলি। যে গাছে বসে আছিস তার ডাল কাটলে পড়ে মরবি।”
বেলা চোখ পাকিয়ে বলল, “আমি তোর গাছে বসে আছি?”
“এখন পর্যন্ত নয়। তোর মামামামির গাছের ডালে বসে আছিস।”
“তা হলে শাসাচ্ছিস কাকে!”
শানু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। কাঁধ নাচিয়ে বলল, “এখন যে ডালে বসে বসে দানা খাচ্ছিস তাদের বিপদে তোর কোনো চেতনা নেই।” বলেই নিজের লাগসই ভাষা সংশোধন করে নিল, “আসন্ন বিপদে ক্রাইসিস।”
বেলা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বলল, “আমি ডাক্তার?”
“কে বলেছে! কিন্তু তুই যেভাবে পাল তুলে চলে যাচ্ছিস মনে হচ্ছে—তোর কোনো দুর্ভাবনা নেই।”
বেলা যেন এবার একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল। কপালের চুল সরিয়ে শানুকে দেখতে দেখতে বলল, “আমি কী করব?”
“ভাব। একটা উপায় ভাব।”
“আমার মাথায় আসে না।”
“তা হলেও ভাব। আমিও ভাবছি। মেসোকে এভাবে আপসেট হতে দেওয়া যায় না। মানুষটা ভয়েই আধমরা হয়ে গেছে। আর মাসির অবস্থা দেখলি, এক বেলাতেই তিরিক্ষে। এভাবে দশটা দিন চললে এ বাড়িতে আর তিষ্ঠোতে হবে না।”
বেলারও মনে হল, মামিকে সামলাতে না পারলে বাড়িতে একটা বিশ্রী ব্যাপার হবে। মামির যা মেজাজ আর মুখ।
বেলা বলল, “বেশ ভাবছি আমি। তুইও ভাব।”
“ও কে।—লেট মি থিংক!”
বেলা তার নিজের ঘরে চলে গেল।
তিন
সুবোধ ডাক্তার যথাদিনে যথাসময়ে এসে হাজির। রবাির সন্ধেবেলায়।
পরনে মিহি দিশি ধুতি, গায়ে পাঞ্জাবি, হাতে বাহারি ছড়ি, মুখে সিগারেট। দোতলায় উঠতে উঠতে সুবোধ ডাক্তার হাঁক পাড়লেন, “কই হে গুরুপদ শুয়ে আছ নাকি?”
এ- বাড়িতে সুবোধের অবারিত দ্বার। তবু তিনি আসার সময় ষষ্ঠীচরণ ডাক্তারবাবুকে দেখতে পেয়েছিল। আসুন আসুন করে ডেকে এনে দোতলার একপাশে বসার ঘরে বসাল।
বাতি জ্বলছিল ঘরের, পাখাটা চালিয়ে দিল। দিয়ে বাড়ির কর্তাকে খবর দিতে ছুটল।
সুবোধ ডাক্তার বসতে না বসতেই শশিতারা ঘরে এলেন। সদ্য গা ধুয়ে মাড় করকরে সাদা খোলের শাড়ি পরনে। মুখে পান। এসেই বললেন, “তুমি ডাক্তার, না, থানার দারোগা?” বলে সুবোধের সাজগোজ লক্ষ করতে লাগলেন।
সুবোধ হেসে বললেন, “দেখে কি দারোগা মনে হচ্ছে?”
মাথা নেড়ে শশিতারা জবাব দিলেন, “দেখে তো মনে হচ্ছে বুড়ো কার্তিক।”
হো হো করে হেসে উঠলেন সুবোধ। মাথার চুল দেখিয়ে বললেন, “এখনো চুল পাকেনি, দাঁত পড়েনি। বুড়ো বোলো না, বলল বাবু কার্তিক।”
শশিতারা ঠোঁট ওলটালেন। “বাবুই বটে। গিয়েছিলে কোথায়? সাজগোজের অত ঘটা!”
সুবোধ বললেন, “ঘটার কী দেখলে! রবিবার সন্ধেবেলায় আমি পুরো বাঙালিবাবু। তুমি যেন নতুন দেখছ।”
“না, তা দেখছি না। তবু আজ একেবারে—”
“ও! চোখে পড়েছে তবে! —তবে বলি, ফিরতি পথে একটা বিয়েবাড়ি হয়ে নিজের ডেরায় ফিরব। দেখা করে যাব। —তা উনি কোথায়, তোমার কর্তা?”
“আসছে।” শশিতারা এবার সরে গিয়ে একটা সোফায় বসলেন। “তুমি যে আমার কথার জবাব দিলে না? আমি জানতে চাইছিলাম—তুমি ডাক্তার না দারোগা? ওই ভিতু মানুষটাকে আধমরা করে ছেড়ে দিয়েছ!”
সুবোধ হেসে বললেন, “তুমি যে মানুষটাকে পুরো মেরে ফেলার ব্যবস্থা করেছ! কী করেছ গুরুপদকে—তুমি নিজেই জানো না! তোমার নামে মামলা ঠুকে দেওয়া উচিত।”
শশিতারা হাতের ঝটকা মেরে বললেন, “বাজে বকো না! মামলা আমি তোমার নামে ঠুকব। ডাক্তার হয়ে একটা মানুষকে অকারণ ঘাবড়ে দিয়ে ভয় পাইয়ে মারার চেষ্টা করছ।”
এমন সময় গুরুপদ ঘরে এলেন। তেল ফুরিয়ে যাওয়া বাস-মিনিবাসের মতন গড়িয়ে গড়িয়ে।
সুবোধ বললেন, “এসো।” বলে গুরুপদকে দেখতে লাগলেন।
গুরুপদ সোফার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, “তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম। স্নানটা সেরে এলাম। বড্ড গরম।”
সুবোধ বললেন, “আছ কেমন?”
সোফায় বসলেন গুরুপদ। বললেন, “আর থাকা! পরশু সারা রাত ঘুম হল না। কাল আর বাড়ির বাইরে বেরোইনি। আজ রবিবার। বসে বসেই কাটছে। বড্ড দুর্বল লাগছে হে। মাথায় থেকে থেকে চরকি মারছে।”
সুবোধ এবার শশিতারার দিকে তাকালেন। “ওকে উপোস করাচ্ছ নাকি?”
“আমি কি করাচ্ছি! নিজেই করছে!”
“কিছুই খাচ্ছে না?”
“ওই একটু শরবত, ফল, মিষ্টি।”
“ভাতটাত খাচ্ছে না? মাছ মাংস, লুচি?”
“কই আর! মুখে তুলছে। খাবে কেমন করে, তুমি ওকে সমন ধরিয়ে দিয়েছ।—মুখে উঠছে না—তবু মুখ কামাই নেই। আমায় দুষছে। “
সুবোধ হেসে বললেন, “পেয়াদার কাজ পেয়াদা করেছে, আমি তো আর কোর্ট নই।—যাক গে, কাজের কথা বলি তুমিও শুনে রাখো, শশি!” বলে সুবোধ পকেটে হাত দিয়ে একটা খাম বার করলেন। তার মধ্যে গুরুপদর রিপোর্টের কাগজগুলো ছিল। খামটা সেন্টার টেবিলের ওপর ফেলে দিলেন সুবোধ। বললেন, “সেদিন তোমায় যা বলেছিলাম আজও বলছি। তোমার অনেক আগে থেকেই সাবধান হওয়া উচিত ছিল। শরীরটাকে বাইরে ফুলিয়েছ, ভেতরে সবই গোলমাল। এখন থেকে যদি স্ট্রিকলি সাবধান না হও—বিপদে পড়বে।”
শশিতারা বললেন, “হয়েছে কী?”
সুবোধ বললেন, “কোনটা হয়নি! ব্লাড প্রেশার, সুগার, কোলেস্টরাল— ভাবাই যায় না । হার্টও ঝিমিয়ে পড়ছে। হার্টের অপরাধটা কী! বোঝা বইতে পারছে না। তাকে ফাংশান করার পথ খোলা রেখেছ?”
গুরুপদ বললেন, “যা হবার হয়েছে—এখন কী করতে হবে বলো?”
সুবোধ এবার পাঞ্জাবির অন্য পকেট থেকে দুটো কাগজ বার করলেন বললেন, “যা করতে হবে আমি লিখে দিয়েছি। ওষুধপত্র যা খাবে তার জন্যে একটা কাগজ। অন্যটা হল তোমার খাওয়াদাওয়ার চার্ট। যেমনটি আছে তেমনটি ফলো করবে। আপাতত পনেরো দিন তারপর একমাস। আমি দেখব, অবস্থাটা কী দাঁড়ায়। পরের ব্যবস্থা পরে। তোমরা যদি আমার ওপর খবরদারি করো, আমি কিন্তু কোনো দায়িত্ব নেব না। অন্য ডাক্তারের কাছে যাবে। অ্যাজ ইউ লাইক।”
গুরুপদ একবার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন, তারপর বন্ধুর। বললেন, “তুমি রাগ করছ কেন? আমি ভাই, তোমার অ্যাডভাইস মতন চলতে চাই। যা যা বলে দেবে করব।” বলে স্ত্রীকে দেখালেন, “খোদকারি যা করার উনি করেন, ওঁকে বলো।—বাট আই সে, আর খোদকারি সহ্য করব না।”
সুবোধ শশিতারার দিকে তাকালেন।
শশিতারা বললেন, “বা! যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর।”
সুবোধ বললেন, “শশি, তুমি গুরুপদর বউ হতে পার, ডাক্তার নও। তোমার সব ব্যাপারে নাক গলানো উচিত নয়। আমার কথা মতন না চললে আমি কিন্তু এই পেশেন্ট আর দেখব না!”
গুরুপদ বলেন, “না না, এ তুমি কী বলছ! আমি ভাই, তোমাকে বিশ্বাস করি। হাই হাই ডাক্তার কলকাতায় অনেক আছে। তাতে আমার কী! তুমি আমার ধাত জানো, তোমার দেওয়া ওষুধ খেলাম এতদিন। বাঁচি তোমার হাতেই বাঁচব, মরি তোমার হাতেই মরব।”
মাথা নাড়লেন সুবোধ। না, আমার হাতে মরতে হবে না।”
শশিতারা এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। স্বামীর দিকে তাকাচ্ছিলেন একবার, অন্যবার সুবোধকে দেখছিলেন। স্বামী কেমন ঝট করে বন্ধুর দিকে হেলে গেলেন। গোটা দোষটাই যেন শশিতারার। রেগে গেলেন শশিতারা। বললেন, “তোমরা যা বলছ তাতে মনে হচ্ছে আমিই স্যান্ডেলবাবুকে মারছি।”
সুবোধ ঠাট্টা করে বললেন, “নিজেও মরছ।”
“আমি মরছি?”
কথাটা মাঝখানে থেমে গেল। চা এসেছে। মানিক আর ফেলু—ট্রের ওপর চায়ের কাপ সাজিয়ে, জলের গ্লাস মিষ্টির প্লেট নিয়ে ঘরে এল। এসে সেন্টার টেবিলের ওপর রাখল।
শশিতারা বললেন, “ঠিক আছে। তোরা যা।”
মানিক আর ফেলু চলে গেল। ফেলু একেবারে বছর তেরো-চোদ্দোর বাচ্চা। শানু তার নাম দিয়েছে ‘গুলতি।‘
শশিতারা বললেন, “যা বলছিলাম। আমি মরছি—কে বলল?”।
সুবোধ মিষ্টির প্লেট দেখতে দেখতে বললেন, “তোমাদের মোদকের সন্দেশ। সাইজটা ভালই করে। আমাদের ওখানে এর অর্ধেক—।—তা গুরুপদ এই সন্দেশ তোমার বউ তোমায় কটা করে গেলায় রোজ?”
গুরুপদ বললেন, “চার ছটা।”
“বাঃ বাঃ! আর ওই কালোজাম—?”
“কালোজাম আমি খাই না, ছেলেমেয়েরা খায়। গিন্নি খায়। আমি রসগোল্লা খাই, ছানা থাকে বলে।”
সুবোধ বললেন, “তোমার শরীরের মধ্যে চিনি এখন সাড়ে তিনশোর ওপর। তারই মধ্যে ছটা বিরাট সন্দেশ, আট দশটা রসোগোল্লা চালিয়ে যাচ্চ! আবার বলছ, তোমার চিকিৎসা করতে।— আমি তো পারব না ভাই, তোমার গিন্নিকে বলো। ডাক্তারের মেয়ে।”
শশিতারার মাথা গরম হয়ে গেল। বললেন, “না তো কি উকিলের মেয়ে! আমার বাবা চারশো সুগার নিয়ে মাছ মাংস রাবড়ি সন্দেশ-মিহিদানা সব খেত আর গায়ে প্যাঁক করে ইনসুলিন ফুঁড়ত।” বলে শশিতারা ইনজেকশান নেবার ভঙ্গিটা দেখালেন।
সুবোধ চায়ের কাপ উঠিয়ে নিলেন। “তা হলে তো হয়েই গেল, গুরুপদ। তুমি যেমন চালাচ্ছ চালিয়ে যাও—তোমার গিন্নি রোজ প্যাঁক করে ছুঁড়ে দেবে। এ ফোঁড় ফোঁড়।”
আতকে উঠে গুরুপদ বললেন, “পাগল! শশির নিজেরই শরীর খারাপ। হাত পা কাঁপে, ঘাড় মাথা টনটন করে, তার ওপর বুক ধড়ফড়—”
চায়ের আরাম করে চুমুক দিয়ে সুবোধ বললেন, “ঈশ্বরের ইচ্ছেয় উনি তোমার যথার্থ সহধর্মিণী। দাঁড়িপাল্লায় রাখলে তোমরা সমান।”
“আজকালকার দিনে তাই হতে হয়, শশিতারা গম্ভীরভাবে বললেন। বলে হাতের মোট মোটা চুড়ি ঘোরাতে লাগতেন। আঁট হয়ে বসে গেলে কষ্ট হয়।
গুরুপদ সুবোধকে বললেন, “শশি যা বলছে বলুক। আমি তোমার কথা মতনই চলব। যেমন যেমন লিখে দিয়েছ তেমন তেমন করব। তুমি শুধু বলো, আমার কী হয়েছে?”
হাত বাড়িয়ে সুবোধ একটা সন্দেশ নিলেন। বললেন, ‘অত শুনে তোমার লাভ নেই। সোজা কথা যেমনটি বলেছি সেই ভাবে চলো। গায়ের চর্বি কমাও, ওজন কমাও, খাওয়াদাওয়া হিসেব মেপে করো, হার্টটাকে খানিক সামলাতে দাও। তারপর দেখা যাবে কী করা যায়!”
“আমার হার্ট কি খারাপ হয়ে গেছে?”
“যাচ্ছে।”
“তা হলে?”
“হায় হায় করে লাভ নেই। যে জন দিবসে মনের হরষে জ্বালায় মোমের বাতি—সেই রকম আর কি। এত গিন্নির কথায় চোব্য-চোষ্য খেয়েছ—এবার তার ফল ভোগ করছ।”
গুরুপদ হঠাৎ স্ত্রীর দিকে বিরক্তভাবে তাকালেন। বললেন, “আমি আর ওর কথা শুনব না।”
শশিতারা মুখ ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, “পাড়ার পঞ্চার মায়ের কথা শুনো।”
সুবোধ এবার শশিতারার দিকে তাকালেন। বললেন, “কর্তার তো হল। তোমারটাও হোক। একবার চেক আপটা করিয়ে নাও।”
“দরকার নেই”,শশিতারা মাথা নাড়লেন।
“ভাল কথা বলছি। পরে আর চারা থাকবে না।”
“না থাকুক।— তোমার মতন ডাক্তারের খপ্পরে আমি পড়ব না।”
“আমি ডাক্তার খারাপ নই। এম ডি।”
গুরুপদ হঠাৎ বললেন, “শশি তোমাকে কম্পাউন্ডার বলে সুবোধ।”
সুবোধ গলা ছেড়ে বেজায় জোরে হেসে উঠলেন। হাতের চা চলকে গেল। আর একটু হলে গলায় সন্দেশ লেগে বিষম খেতেন।
হাসি থামলে সুবোধ বললেন, “ঠিকই বলে। আমি যখন ফাইনাল ইয়ারের ছাত্র তার আগে থেকে শশির বাবা—বলাই মেশোমশাইয়ের দাবাইখানায় মিক্সচার, মলম তৈরি করতাম। মেশোমশাই বলতেন, ওহে সুবোধ, ওটাকে সুই মেরে দাও। দিতাম। “
শশিতারা বললেন, “তাতেও কিছু হল না।”
চোখে মজার হাসি নিয়ে সুবোধ বললেন, “কই হল! মালাটা গুরুপদর গলায় পড়ে গেল। অবশ্য ভালই হল।” বলতে বলতে হেসে উঠলেন।
গুরুপদও হেসে ফেললেন।
শশিতারাও না হেসে পারলেন না। বললেন, “রঙ্গটাই শিখেছ!”
চা খেয়ে সুবোধ উঠে পড়ছিলেন। “আমি চলি। একটা নেমন্তন্ন বাড়িতে একবার মুখ দেখিয়ে যেতে হবে।”
শশিতারা ধমকের গলায় বললেন, “চলি মানে! মিষ্টিগুলো কে খাবে?”
“গুরুপদকে খাওয়াও। নিজে খাও। আমি মিষ্টিটিষ্টি বড় একটা খাই না তোমরা জান! ঘি নয়, মাখন নয়।— তুমি গুরুপদর লেজ কেটো—আমাকে কাটবার চেষ্টা কোরো না।— চলি, গুরুপদ মন খারাপ কোরো না, তাঁর ইচ্ছেয় সব হয়।— পনেরো দিন পরে আমার কাছে যাবে। বুঝলে?”
সুবোধ দরজার দিকে পা বাড়িয়ে বললেন, “সে দুটো কোথায়? গলা পেলাম না?”
শশিতারাও উঠে পড়েছিলেন। বললেন, “চরতে বেরিয়েছে। চরা ছাড়া তাঁদের আর কাজ কী!”
চার
দিন পনেরো পরে রাত্রে খেতে বসে শানু বলল, “মাসি একজন ভাল ডাক্তারের খোঁজ পেয়েছি।” বলে আড়চোখে বেলাকে দেখে নিল।
শশিতারা গম্ভীর হয়ে বললেন, “ডাক্তার আমার কী করবে?”
“মেসোর কথা বলছিলাম…।”
“যার কথা তাকে জিজ্ঞেস করো।” বলে শশিতারা গজগজ করতে লাগলেন। “আমি কে? আমড়া গাছতলায় নেতা হয়ে বসে আছি। কে শুনবে আমার কথা। চব্বিশ ঘণ্টা ঘড়ি মিলিয়ে সুবোধ ডাক্তারের ওষুধ খাচ্ছে আর আয়নায় নিজের মুখ দেখছে। গিয়েছিল ডাক্তারের কাছে। ডাক্তার নাকি বলেছে, আরও পনেরো দিন চালিয়ে যাও—তারপর কথা। হাঁড়িতে চাল নেই জল ফুটছে—সেই রকম অবস্থা এখন। খাবার কথা বললে দুর্বাশা মুনি হয়ে যায়। এটা বারণ ওটা বারণ, ভাত দু চামচে, রুটি দেড়খানা, এক হাতা চারাপোনার ঝোল, এক টুকরো মাছ, উনি আবার চিকেন বলতে আধ পো ওজনের ছানা বোঝেন, তার স্টু, এক পিস মাংস। মুড়ি দু মুঠো, দু কুচি শশা। মিষ্টি-মাস্টা একেবারে নয়। তেল না, ঘি নয়।—এইভাবেই যদি থাকতে হয় বনে গিয়ে তপস্যা করলেই পারে। সংসার করা কেন।”
বেলা একবার শানুকে দেখে নিল। তার কাজ পোঁ ধরার ; শানুদার সঙ্গে সেই রকম কথা। বেলা বলল, “মামাকে আজকাল যা শুকনো দেখায়।”
“দেখাবে না।” শশিতারা বললেন, “মদ্দ মানুষ একজন। কাজকর্ম আছে, কারখানা আছে। হোক না গাড়ি। তবু পাঁচ জায়গায় ছোটাছুটি রয়েছে। ধকল কি কম শরীরের ওপর। অথচ খাবার কথা বললে তেড়ে আসে। বলে, সুবোধ ডাক্তারের পারমিশান করিয়ে আনো। নিকুচি করেছে তোর সুবোধ ডাক্তারের। অমন ঢের ডাক্তার আমি টেকে গুজতে পারি। ওরা হল অনাহারী ডাক্তার ; না খাইয়ে খাইয়ে রুগিকে হাড় জিরজিরে করে দেয়। তারপর ফক্কা। ” বলে দু হাত ওপরে তুলে তালি দিয়ে ফক্কা বোঝালেন। “ছিল বেশ। সুখে থাকলে ভূতে কিলোল।— আমি কিছু বলব না। বললে তেরিয়া হয়ে যেন মারতে আসে।”
শানু বলল, “মেসোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে। মাসি, তুমি শুধু রাগ করে বসে থাকলে ব্যাপারটা হাতের বাইরে চলে যাবে।”
“যাক।”
“আহা—তুমি বুঝছ না, দেহ বলে কথা। দেহ ঠিকমতো ধরে রাখতে না পারলে—বিলীন হয়ে যায়।”
“কী হয়?”
“বিলীন—” শানু মাথার ওপর হাত ঘোরাল ; ঘুরিয়ে ফাঁকা বাতাস বোঝাল।
শশিতারা শানুকে দেখতে লাগলেন।
বেলা সরল গলা করে বলল, “একজন দেখলে আর একজন ডাক্তারকে দেখানো ঠিক নয়। খারাপ লাগে দেখতে। কিন্তু একবার পরামর্শ নিলে কিসের ক্ষতি।”
সঙ্গে সঙ্গে শানু বলল, “অ্যালোপ্যাথির সঙ্গে কত লোক হোমিওপ্যাথি খায়। হোমিওপ্যাথির সঙ্গে কবিরাজি। সুবোধ মেশোর ওষুধবিসুধ যেমন চলছে চলুক না। তার সঙ্গে যদি ধরো ম্যাগনেট ট্রিটমেন্ট চলে, আটকাচ্ছে কোথায়!” বলে শানু মুরগির ঠ্যাং তুলে নিয়ে মুখে পুরল। বেলাকে ইশারা করে দিল চোখ টিপে।
শশিতারা অবাক হয়ে শানুকে দেখতে লাগলেন। কর্তাকে শশিতারা হপ্তায় অন্তত তিনটে দিন মুরগির ঠ্যাং খাওয়াতেন। এখন আর ভদ্রলোক ঠ্যাং খান না। ছোট একটা টুকরো মুখে দেন ; তাও প্যানপ্যানে স্টুয়ের মাংস। মুরগির পনেরো আনা ছেলেমেয়েদের পেটে যায়। শশিতারার এখানে খানিকটা রাগ আছে।
শানুর কথায় রাগ-টাগ ভুলে শশিতারা অবাক হয়ে ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। “কী ট্রিটমেন্ট?”।
“ম্যাগনেট?” — হাড় চিবোতে চিবোতে শানু বলল।
“সেটা কী?”
বেলা তৈরি ছিল। বলল, “ম্যাগনেট থেরাপি। চুম্বক চিকিৎসা।”
শশিতারা মাথায় হাত দিলেন। গরমের দাপটে চুলের খোঁপা আর ঘাড়ে থাকে না, ক্রমশই মাথায় উঠে যাচ্ছে। বললেন, “সে আবার কী। চুম্বক চিকিৎসা। জীবনে শুনিনি।”
শানু বলল, “আমরাও কি আগে শুনেছি! সেদিন বেলি ইংরেজি কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখেছিল। ফক্কুড়ি করছিল। আমায় দেখাল। আমিও দেখলাম। দেখে ওকে বললাম—” শানু বেলাকে দেখাল, “হাসিস না। ভেরি ইন্টারেস্টিং ব্যাপার। আজকাল কত রকম নতুন নতুন চিকিৎসা বেরুচ্ছে, মান্ধাতা আমলের ট্রিটমেন্ট বাতিল হয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের যুগ। তুই সাইন্স জানিস না, তাই হাসছিস।”
বেলা কিছু বলল না। গম্ভীর হয়ে থাকল। ভেতরে ভেতরে ভয় করছিল। শানুদা এক করতে আরেক না করে ফেলে।
শশিতারা বললেন, “লেকচার থাক। জিনিসটা কী বল?”
শানু বলল, “তোমাকে কাগজ দেখাব?”
“কাগজ? কিসের কাগজ?”
“ডাক্তার পাকড়াশির কাগজপত্র! প্যাম্ফলেট। লিফলেট।— আমি কাগজের বিজ্ঞাপন পড়ে একদিন ডাক্তার পাকড়াশির কাছে চলে গেলাম। ধর্মতলা স্ট্রিটে, তালতলার মুখেই। দোতলায় পাকড়াশির অফিস চেম্বার। দশ বারো জন রোগী বসে আছে। বুড়ো বুড়ো, মাঝবয়েসি, কমবয়েসি। মাড়োয়ারি, বাঙালি।—আমাকে ওদের অফিস থেকে ছাপানো কাগজপত্র দিল। বলল, কাগজে সব লেখা আছে।”
“এনেছিস কাগজগুলো?”
“এনেছি। মন দিয়ে পড়েছি। বেলিকেও পড়িয়েছি।”
শশিতারা গলার তিন ভরি হারের তলায় আঙুল দিয়ে একবার গলার পাশটা চুলকে নিলেন। “কী দেখলি?”
“দেখলাম প্রায় সব রকম রোগই ম্যাগনেট ট্রিটমেন্টে সারানো যায়। কি বল, বেলি?”
বেলা ঘাড় হেলিয়ে বলল, বাত, ব্লাড প্রেশার, মাথা ধরা, মাইগ্রেন, স্পনডিলাইটিস, আরও কত কী!”।
শশিতারা কেমন সন্দেহের গলায় বললেন, “সত্যি? না মাদুলির মতন?” মাদুলির ওপর শশিতারা হাড়ে হাড়ে চটা। এক সময়, যখন বয়স ছিল, পেটে একটা বাচ্চা আসার জন্যে হরেক রকম মাদুলি পরেছেন। দুটো হাত আর গলা মাদুলিতে ছেয়ে গিয়েছিল। পাথরও পরেছেন অনেক রকম। কিস্য হয়নি। এখন আর বাড়িতে মাদুলি ঢুকতে দেন না। তবে পাথর আসে। শশিতারা নিজে এখন একটা সাত রতি মুক্তোর আংটি ছাড়া কিছু পরেন না। স্বামীর হাতে চারটে আংটি। পলা, গোমেদ, পান্না আর মুক্তো। পুরুষ মানুষ, কাজকর্ম, কারখানা, নানান অশান্তি—পাথর ছাড়া চলে কেমন করে!
শানু খেতে খেতে বলল, “ওদের কাগজপত্র পড়ে আমার মনে হল, ব্যাপারটা পুরোপুরি ফেলনা নয়। ম্যাগনেটের ব্যাপারটাই রহস্যময়, মাসি। কেন আছে, কেমন করে আছে, এর রহস্য কেউ ধরতে পারল না। ঠিক কিনা বল, বেলি?”।
বেলা বিজ্ঞান পড়ে না। কিন্তু শানুর কাছে শুনে রেখেছে। মাথা নেড়ে বলল, “মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মতন।”
“একজ্যাক্টলি। ইট ইজ দেয়ার বাট হাউ? ইট ইজ এ মিষ্ট্রি।— জানো মাসি, সেদিন টিভি-তে একটা প্রোগ্রাম দেখাচ্ছিল। বিদেশে এখন রোগ ধরার জন্যে ম্যাগনেটিক ডিটেকটার ব্যবহার করছে। দারুণ দেখাচ্ছিল।”।
শশিতারা বললেন, “অত শুনে আমার দরকার নেই। কী করে চুম্বক নিয়ে তাই বল।”
“কিচ্ছু না। রোগ বুঝে ওজন মতন ম্যাগনেট পিস বডিতে বেঁধে দেয়। নর্থ পোল, সাউথ পোল। ব্যাস ওতেই—। আসলে ট্রিটমেন্টের ব্যাপার তো লিখে দেবে না; এটা তো ডাক্তারদের ব্যাপার!”
“এ রকম চিকিৎসা আর কোথায় হয়?”
“বম্বে ; দিল্লি। —বিদেশে অনেক জায়গায়।”
শশিতারা এবার উঠবেন। ছেলেমেয়েদের খাওয়াও শেষ হয়েছে। বললেন, “বেশ, তোরা বল ওঁকে। আমি বলব না।”
শানু বলল, “বাঃ! তুমি না বললে—”
বেলা বলল, “মামি, আমরা বললে মামা কানেই তুলবে না। তোমারই বলা ভাল। তারপর যা করার শানুদা করবে।”
মাথা নাড়লেন শশিতারা। “আমি কিছু বললেই খ্যাঁক খ্যাঁক করে ওঠে। ভাবে, আমি তোর মামার সর্বনাশ করার জন্যে মন্ত্র দিচ্ছি! ওই সুবোধ ডাক্তার যে কী বুঝিয়ে দিয়ে গেল। তোমার মামা-মেশোর ধারণা হল, আমার জন্যেই ওর শরীরের এই অবস্থা! এখন আমি শত্রু।”
বেলা বলল, “আমরা সবাই বলব। তুমি, শানুদা, আমি।”
শশিতারা উঠে পড়লেন। বললেন, “ঠিক আছে, বলে দেখো। এই মানুষ আমায় সারা জীবন জ্বালাচ্ছে, আরও জ্বালাবে। যেমন কপাল আমার।”
শানু আর বেলা চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে মুখ টিপে হাসল।
খাওয়ার দাওয়ার পর ঘরে ফিরে এসে শানু বলল, “বেলি কাল তুই তোর মামাকে ক্যাচ কর। তোকে অত ভালবাসে, না করতে পারবে না। জোঁকের মতন লেগে থাকবি—আদিখ্যেতা করবি, কাঁদবি—”
বেলা বলল, “তুই গিয়ে লাগ না!”
“আমার দ্বারা হবে না। তুই মেয়ে। মামার ভাগ্নি। তুই পারবি। তোকে ভদ্রলোক জেনুইন ভালবাসে।— তা ছাড়া কেসটা তোর—তোকে লেগে থাকতে হবে।
বেলা তার সরু বুড়ো আঙুলটা দেখাল! পরে বলল, “তোর কি চোখ নেই! তুই দেখছিস মামিই এখন পাত্তা পাচ্ছে না। মামার কাছে তো আমি—!”
শানু বনেদি চালে একটা সেঁকুর তুলল। তুলে সিগারেটের প্যাকেট খুঁজতে খুঁজতে বলল, “কিসের একটা কথা আছে না রে টুথ ইজ স্ট্রেঞ্জার দ্যান ফিকশান— আমি দেখছি মানুষের কারবার গল্পকেও হার মানায়।” বলতে বলতে শানু সিগারেট ধরিয়ে বড় করে ঢোঁক গিলল। “যে মাসি মেসোকে মুঠোয় পুরে রেখেছিল সেই মেসোই এখন মাসিকে হাঁকিয়ে দিচ্ছে! ভাবা যায়।—তুইও কম যাস না!”
শানুর কথাটা বোধ হয় মিথ্যে নয়। অন্তত গুরুপদ আর শশিতারাকে দেখে তেমন মনে হতে পারে। যে গুরুপদ একমাত্র ব্যবসা ছাড়া উঠতে বসতে খেতে শুতে স্ত্রীর কথায় চলতেন ফিরতেন—এত বছর চলেছেন—হঠাৎ তিনিই এখন স্ত্রীর ওপর বেজার। মাঝে মাঝে রাগে ফুসেও উঠছেন। গুরুপদর যেন এতকাল পরে চৈতন্যোদয় হল। দেখলেন, শশিতারার আদর আতিশয্য ধমক হুকুম মেনে চলে চলে তাঁর অবস্থা কাহিল হয়ে গিয়েছে। গুরুপদর এই ভয়াবহ শারীরিক অবস্থার জন্যে শশিতারাই যেন দায়ী। খাও খাও করেই তাঁর জীবনটা শেষ করে দিলেন শশিতারা। আর নয়। গুরুপদ এখন স্ত্রীর কথা কানেই তুলছেন না, উলটে নিজেই ধমক মারছেন।
বেলা বলল, “তুই ভাবছিস কেন! মামিই রাজি করিয়ে দেবে।”
“দিলে ভাল। না দিলে ওয়ে আউট বার করতে হবে।” বলে শানু গিয়ে বিছানায় বসে পড়ল। সিগারেটে টান মারতে মারতে বলল, “বেলি, তুই শুধু মাসির ভরসায় বসে থাকলে পারবি না। নিজে একটু লেগে পড়। ইনসিয়েটিভ নে।”
“মানে?”
“মেসো সিরিয়াসলি ভয় পেয়ে গেছে। ভয় পেয়েছে বলেই মাসির ওপর খাপ্পা হয়ে গেছে। মাসি এখন বিরোধী পক্ষ। তুই তোর মামার পক্ষ নে।”
“রেখে দে।—মামিকে তুই চিনিস না। কদিন সবুর কর—দেখবি।”
“দেখব।— তুই কাল তোর মামাকে মিট করছিস? ছাদে মিট করবি। তোর মামা যখন ফুলের টবে জল দেয় তখন। মনটা সেসময় নরম থাকবে।”
বেলা চেয়ারে বসে পা দোলাতে দোলাতে বলল, “সে আমি করব। কিন্তু তারপর?”
“কিসের তারপর?”
“যদি মামা রাজি হয়ে যায়?”
“ম্যাগনেট ট্রিটমেন্ট হবে।”
বেলা নজর করে শানুকে দেখতে লাগল। বলল, “হলে তো মরব।”
শানু অবাক হাঁ করে বেলাকে দেখতে লাগল! বলল, “তুই বকছিস কী! ম্যাগনেটে কেউ মরে! তোকে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি। ফাঁসি হতে পারে, মরবি না।”
“আমি কিছু বুঝতে পারছি না।”
শানু বিছানা থেকে উঠে পড়ল। বলল, “বেলি, তুই ডোবাবি। তোকে এত করে বোঝালাম তিন পা এগিয়ে এক পা পিছিয়ে এসে লাভ হবে না। তোকে এগুতে হবে।”
বেলা বলল, “মামা যদি জিজ্ঞেস করে, ম্যাগনেটে রোগ সারে কেমন করে?”
“বলবি, সারে নিশ্চয়। ম্যাগনেটের একটা এফেক্ট আছে। ডাক্তার ওসব বুঝবে—তুই আমি কী বুঝব! আমরা পেনিসিলিন পর্যন্ত জানি। ম্যাগনেট আরও অ্যাডভান্স। পঞ্চাশ বছর পরে দেখবি—এম ডি উঠে যাবে, তার বদলে ডাক্তাররা হবে ডক্টর অফ ম্যাগনেটিক থেরাপি।”
বেলা হাই তুলতে তুলতে বলল, “ততদিন আমি বেঁচে থাকব না।”
“বলিস কী! তুই সত্তরের আগে মরবি? একেবারেই নয়। তুই ঝুনো বুড়ি হবি, তোর দাঁত পড়বে, মাথার চুল সাদা হয়ে যাবে, লাঠি নিয়ে নিয়ে হাঁটবি, চোখে দেখতে পাবি না, শুকনো আমসি হয়ে মরবি।”
“আর তুই মরবি?”
“আমি।—আমি বোধ হয় ছেঁড়া জুতোর সোল হয়ে।”
বেলা বলল, “না, তুই মরবি পিপড়ে ধরা বাতাসা হয়ে।” বলতে বলতে বেলা হেসে উঠল।
শানুও হেসে ফেলল।
হাই তুলতে তুলতে বেলা উঠে পড়ল এবার। তার ঘুম পাচ্ছে।
চলে যাচ্ছিল বেলা, শানু বলল, “কাল সকালে লেগে পড়বি।”
পরের দিন বেলা দশটা নাগাদ শানুর ডাক পড়ল তেতলায়।
গুরুপদ চেয়ারে বসে আছেন। শশিতারা হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে।
শানু মাঝামাঝি জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল।
গুরুপদ শানুকে দেখতে দেখতে বললেন, “ডাক্তারের নাম?”
“পাকড়াশি।”
“পুরো নাম?”
“এম পাকড়াশি।”
“ছোকরা?”
“দেখিনি। কাগজপত্র নিয়ে চলে এসেছি।—ছোকরা নয় বোধহয়। অতগুলো ডিগ্রি ডিপ্লোমা।”
“ট্রিটমেন্টটা কী রকম?”
শানুর মনে হল, মেসোর গলা একটু নরম। বলল, “আমি প্যাম্ফলেট পড়ে যা দেখলাম, ম্যাগনেটের টুকরো বেঁধে দেয় শরীরে। অন্য কিছুও থাকতে পারে জানি না।”
“কত বড় টুকরো?”
“অসুখ আর অবস্থা বুঝে।”
“আর কিছু নয়?”
“আবার কী?”
“খাওয়া দাওয়া ওষুধ?”
“জানি না। বোধহয় তেমন কোনো রেস্ট্রিকশন নেই।”
“ফোন নম্বর আছে ডাক্তারের?”
“আছে।”
“একটা কল দিয়ে দাও। বাড়িতে এসে দেখে যাক।”
শানু একবার শশিতারার দিকে তাকাল। তারপর মাথা নেড়ে চলে গেল।
সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় শানু লাফ মেরে মেরে নামছিল।
পাঁচ
এম পাকড়াশির পুরো নাম মহাদেব পাকড়াশি। দেখতে যাত্রাদলের মহাদেবের মতন। তফাতের মধ্যে যাত্রাদলের মহাদেব বাঘছালের বদলে গেরুয়া রঙে ছোপ ছোপ ছাপানো খাটো কাপড় পরে, লুঙির মতন করে, মহাদেশ পাকড়াশি পরেন গ্যালিস দেওয়া প্যান্ট। নয়তো ভুড়ি থেকে প্যান্ট নেমে যায়।
মহাদেব পাকড়াশি বাড়িতে রোগী দেখতে আসেন না। তাঁর চেম্বারে গিয়ে দেখিয়ে আসতে হয়।
গুরুপদকেও যেতে হল। সঙ্গে শানু।
শশিতারা বায়না ধরলেন, তিনিও যাবেন। শানু ছেলেমানুষ। সব কথা গুছিয়ে বলতে পারবে না। ডাক্তার বলবে এক, শুনবে অন্য আর। গুরুপদ তো ভিতুর বেহদ্দ। একজন শক্ত লোক থাকা দরকার, যে সামলাতে পারবে, কথা বলতে পারবে।
কাঁটায় কাঁটায় সোয়া ছটায় গুরুপদরা হাজির হলেন মহাদেব পাকড়াশির চেম্বারে। গিয়ে দেখেন, জনা তিনেক রোগী বসে আছে। একটা চৌকো ঘরে। ঘরে বাতি জ্বলছে, পাখা চলছে। কতকগুলো পুরনো ম্যাগাজিন ফরফর করে উড়ছে। রোগীদের মধ্যে দুই জেনানা। গায়ে গতরে শশিতারাকে ছাপিয়ে যায়। তৃতীয় জন এক অ্যাংলো ইন্ডিয়ান। অম্বুলে চেহারা।
জেনানাদের দেখে শশিতারা নিচু গলায় বললেন, “সার্কাসের হাতি”। গুরুপদ বললেন, “চুপ। শুনতে পাবে। এরা কলকাতার মাড়োয়ারি। বাংলা বোঝে।”
সাড়ে ছটায় ডাক পড়ল গুরুপদর। অ্যাপয়েন্টমেন্ট করা ছিল আগেই।
গুরুপদ সদলবলে ডাক্তারের ঘরে ঢুকে পড়লেন।
ঘরে ঢুকে গুরুপদ যাকে দেখলেন তাঁকে ডাক্তার বলে মনে হল না।
গুরুপদ নমস্কার করলেন। শশিতারার দেখাদেখি শানুও হাত তুলল।
“আপনারা সবাই—?”
গুরুপদ বললেন, “আমার স্ত্রী। আর আমার শালীর ছেলে। আমার সঙ্গেই এসেছে।”
“বসুন।”
গুরুপদরা বসলেন।
মহাদেব তাঁর ঝাঁকড়া মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে নিলেন। ঝুলঝাড়া লাঠির আগায় যেমন শনের আঁটি থাকে মহাদেবের মাথার চুল সেই রকম দেখাচ্ছিল। অবশ্য রঙে। ঢঙে নয়। ঢঙে যাত্রাদলের মহাদেবের মতন ফাঁপানো।
মহাদেব বললেন, “আপনি পেশেন্ট?”
“আজ্ঞে হা।”
“কী হয়েছে আপনার?”
“প্রেশার, সুগার, কোলেস্টরাল, হার্ট, পাইলস—।”
“বাবা! এ যে পঞ্চবাণ!”
“আজ্ঞে?”
“না বলছি, পঞ্চবাণে বিধে ফেলেছে যে!”
শশিতারা ফিস ফিস করে শানুকে বললেন, “কাগজগুলো দেখা। পরীক্ষার কাগজগুলো।”
শানুর কাছেই পরীক্ষার কাগজগুলো ছিল। ডাক্তারের সামনে এগিয়ে দিল।
মহাদেব কাগজগুলো দেখলেন না। না দেখে গুরুপদকেই দেখতে লাগলেন।
“কী নাম যেন আপনার?” মহাদেব বললেন।
“গুরুপদ সান্যাল।”
“থাকেন কোথায়?”
“পাইকপাড়ায়।”
“হুঁ!” এবার পাতা উলটে উলটে কাগজগুলো একবার দেখলেন মহাদেব। চোখ বোলালেন। “কত বয়েস হল?”
“তা বছর বাহান্ন!”
মহাদেব কথা বলতে বলতে পট পট করে দু চারগাছা চুল ছিড়লেন নিজের মাথার। এটা তাঁর মুদ্রাদোষ।
“ফিফটি টু। তা হলে দাঁড়াচ্ছে ছাব্বিশ। সিকি দাঁড়াচ্ছে তেরো। দশে এক হলে— দাঁড়াচ্ছে এক কেজি আর তিনে তিনশো গ্রাম মতন—”
গুরুপদ কিছুই বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন।
মহাদেব এক টুকরো কাগজে পেনসিল দিয়ে কিসের হিসেব নিকেশ সারতে সারতে বললেন, “আপনি কী ধরনের ট্রিটমেন্ট চান। শর্ট অর লং?”
গুরুপদ বোকার মতন ডাক্তারকে দেখতে দেখতে বললেন, “বুঝলাম না।”
‘বুঝিয়ে দেব। সবই বুঝিয়ে দেব”, মহাদেব বললেন। বলে টেবিলের ওপর রাখা একটা মোটা মতন ছাপানো কাগজ তুলে নিলেন। “আপনি দেখবেন, না, আমি বলে দেব?”
“আপনিই বলুন।”
“আমাদের এখানে ট্রিটমেন্টের দুটো গ্রুপ আছে। কোর্স বলতে পারেন। শর্ট অ্যান্ড লং। শর্ট হল ছ সপ্তাহ থেকে দশ সপ্তাহের মতন। লং হল—থ্রি টু সিক্স মাস। যে যা পছন্দ করে।”
শশিতারা আর শানুর দিকে তাকালেন গুরুপদ।
শশিতারা বললেন মহাদেবকেই, “উনি কাজের মানুষ। তাড়াতাড়ি যা করা যায় করতে হবে।
মহাদেব বললেন, “তা হলে দাঁড়াচ্ছে ছয় থেকে দশ।” বলে দু-পাশে ঘাড় দোলাতে লাগলেন। “ছয়ে হবে বলে মনে হয় না। অতগুলো রোগ। দশও কম হল। আরও দু এক উইক বেশি লাগতে পারে। যাক, সে পরের কথা।”
শানু এতক্ষণ চুপ করে ছিল এবার ফট করে বলল, “স্যার, শর্ট কোর্স ট্রিটমেন্টের রেজাল্ট কী রকম?”
“খারাপ নয়। ভাল।— তবে শর্টে পেশেন্টকে বেশি স্ট্রেইন নিতে হয়। চাপ বেশি থাকে।” বলে গুরুপদর দিকে তাকালেন মহাদেব। “আপনি শর্টই নিন। পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা।”
শানু বলল, “ট্রিটমেন্টটা—! মানে কীভাবে—”।
“বলছি। সবই দেখাচ্ছি।” বলতে বলতে মহাদেব ঘণ্টি টিপলেন। বেয়ারা এল।
মহাদেব বললেন, “জুনিয়ারকে ডাকো। দেখো ঘর ফাঁকা হয়েছে কিনা?”
মহাদেব উঠে পড়লেন। উঠে ডানদিকে এগিয়ে গিয়ে দেওয়ালের কাছে দাঁড়ালেন। জানলার পরদার মতন পরদা ঝুলছিল একপাশে। সরসর করে পরদা সরিয়ে গুটিয়ে ফেললেন।
গুরুপদরা অবাক হয়ে দেখলেন, দেওয়ালের গায়ে একটা বোর্ড। ব্ল্যাক বোর্ডের মতন কালো কুচকুচ করছে। বোর্ডের মধ্যে দুটি মানুষের চেহারা। একপাশে পুরুষ, অন্য পাশে মেয়ে। স্বাস্থ্য বইয়ে নারী পুরুষের ছবি যেভাবে আঁকা হয় সেইভাবে। শুধু আউট লাইন। তবে সাদা খড়ি বা রঙিন পেনসিলে আঁকা নয়, চকচকে কোনো বস্তু বোর্ডের মধ্যে গেঁথে দিয়ে চেহারা দুটি করা হয়েছে।
মহাদেব বাড়তি আলো জ্বেলে দিলেন। দিয়ে আরও একটা সুইচ টিপলেন। বললেন, “নাউ লুক অ্যাট দিস ফিগার। “ বলে পুরুষ চেহারাটা দেখালেন। “আমরা যখন আপনার চিকিৎসা শুরু করব—তখন কতকগুলো পয়েন্ট বেছে নেব। যেমন—এই হল হার্ট—দেখতে পাচ্ছেন। এখানে আমরা দু পিস ম্যাগনেট প্লেস করব। নেক্সট করব, হিয়ার অ্যান্ড হিয়ার দু দিকেই—কোমরের দু পাশে— রাইট অ্যান্ড লেফট সাইডে। তারপর নামব। হাঁটুতে—বোথ সাইডস। আর একটা পিস থাকবে বিটুইন দি শোলডার ব্লেডস। •…তার মানে— আপনার শরীরে অল টোটাল লাগছে দুই আর দুই চার, প্লাস হাঁটুতে দুই—ছয়, আর ঘাড়ে এক—মানে সাত পিস।” বলতে বলতে মহাদেব টেবিলের কাছে এসে হিসেবের কাগজটা দেখলেন। বললেন, “আপনার বডি ওয়েট আর বয়েসের একটা আন্দাজ করে নিয়ে দেখছি—ইউ রিকোয়ার তেরোশো গ্রাম ম্যাগনেট পিস। ওজনটা হচ্ছে লোহার টুকরোগুলোর। ম্যাগনেট স্ট্রেংথ আলাদা। সেটা আপনারা বুঝবেন না। ওটা আমরা নিজেরা করে নিই। চার্জ দিয়ে। ইলেকট্রো ম্যাগনেট।”
এমন সময় ছিপছিপে চেহারার একটি ছেলে এসে দাঁড়াল। দেখতে বেশ। পঁচিশ ছাব্বিশ বয়েস। চোখে ধরার মতন চেহারা। শানু যেন খুঁটিয়ে ছোকরাকে দেখতে লাগল।।
মহাদেব বললেন, “আমার ভাইপো। জুনিয়ার মহাদেব। ওর নাম মুরলী। ও আমার অ্যাসিসটেন্ট। হাতে কলমে যা করার ওই করে।” বলে মহাদেব তাঁর জুনিয়ারকে বললেন, “একটু দেখিয়ে দাও। হার্ট, ওয়েস্ট, নী—আর ঘাড়।”
জুনিয়ার—মানে মুরলী সেই বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল। গিয়ে নিজের অ্যাপ্রনের পকেট থেকে দাবার গুটির মতন গোল লাল গুটি বার করল। পাতলা, ছোট সাইজের। বার করে বোর্ডের ছবির জায়গায় জায়গায় ছুইয়ে দিল। দিতেই গুটিগুলো আটকে গেল।
শানু বলল, “ম্যাগনেট?”
“হ্যাঁ।”
“বাঃ।” বলে শশিতারার দিকে ঘাড় ফেরাল। “মাসি, পুটুসকে আমরা যেই যে ব্যাঙ ঘড়ি কিনে দিয়েছিলাম, জন্মদিনের, আলমারির গায়ে আটকে রাখত—সেই রকম।”
শশিতারা বললেন, “মানুষ তো লোহার আলমারি নয়।”
মহাদেব বললেন, “আটকে রাখার ব্যবস্থা আমাদের আছে।…জুনিয়ার—এঁকে নিয়ে যাও। বুথে বসাও।” বলে গুরুপদর দিকে তাকালেন, “আপনাকে কি নিয়ে গিয়ে ম্যাগনেটগুলো বসিয়ে দেবে?”
গুরুপদ থতমত খেয়ে বললেন, “এক্ষুনি?”
“আপত্তি কী! আজই বসিয়ে দিক।— ভয় পাবার কিছু নেই। আপনি আজ থেকেই শুরু করুন। দিন সাতেক পরে একবার আসবেন। একবার ম্যাগনেটিক ওয়াশ দেব।”
জুনিয়ার গুটিগুলো তুলে নিল। নিয়ে সুইচ বন্ধ করল।
শানু বলল, “পিসগুলো ছোট ছোট হবে?”
“তা কেমন করে হয়।” মহাদেব বললেন, “তেরোশো গ্রাম টোটাল ওয়েট। এ তো চন্দনের ফোঁট্টা নয়।”
গুরুপদ স্ত্রীর দিকে তাকালেন।
শশিতারা বললেন, “গিয়ে দেখো। অসুবিধা হলে বলতে পারবে। ”
শানু বলল, “জুতোর দোকানে গেলে পায়ের সঙ্গে জুতো ফিট করিয়ে নিতে হয়। সেই রকম আর কি।”
বাধ্য হয়েই গুরুপদ উঠে দাঁড়ালেন।
জুনিয়ার মানে মুরলী বলল, “আসুন।”
গুরুপদকে নিয়ে মুরলী পাশের ঘরে চলে গেল।
মহাদেব নিজের চেয়ারে বসলেন। বললেন, “একটা কাজ করা যেতে পারে। মাঝে মাঝে পিসগুলো চেঞ্জ করার দরকার হয়। সে-কাজটা না হয় বাড়িতে গিয়েই করে দিয়ে আসবে জুনিয়ার। তবে বার তিনেক ম্যাগনেটিক ওয়াশ, বার দুই ট্রেমার দিতে হবে। ওটা বাড়িতে হবে না। এখানে আসতে হবে।”
শানু বলল, “ইয়ে মানে, উপকারটা কখন থেকে বোঝা যাবে?”
“হপ্তা খানেক পর থেকে একটু একটু বোঝা উচিত। সেকেণ্ড উইকের পর সিওর।”
“ছ সপ্তাহ পর থেকে—”
“ভাল ইমপ্রুভমেন্ট হবে।”
শশিতারা বললেন, “খাওয়াদাওয়া? —আজকাল কিছুই খায় না।
“ “কেন?”
“ভয়ে।”
মহাদেব হাসলেন নিজেকে দেখালেন। বললেন, “আমি সব খাই, আমার বয়েস পঞ্চাশ। হ্যাঁ, বয়েসে একটু রেস্ট্রিকশান দরকার। তার মানে একাদশী করা।—আপনি একটু দেখেশুনে খেতে দেবেন। ব্যাস আর কী!”
শশিতারা যেন খুশি হলেন।
হঠাৎ মহাদেব বললেন, “আচ্ছা, মিস্টার সান্যাল কি কখনো গড়পারের দিকে থাকতেন?”
শশিতারা অবাক। বললেন, “গড়পারেই তো থাকতেন। ওদের বাড়ি ছিল। শরিকি বাড়ি। আপনি কেমন করে জানলেন?”
মহাদেব হেসে বললেন, “ধরেছি ঠিক। আমরা একই স্কুলে পড়তাম। স্কটিশ স্কুলে।”
শশিতারা মাথার কাপড় গোছাতে গোছাতে বললেন, “ওমা! দেখছ!”
মহাদেব বললেন, “আমি ওঁর চেয়ে জুনিয়ার ছিলাম। —চেহারাটা পালটে গিয়েছে। কিন্তু মুখ দেখে কেমন মনে হল—।”
শানু বলল, “একেই বলে কোয়েনসিডেন্স!”
মহাদেব টেবিল চাপড়ে বললেন, “কিছু ভাববেন না বউদি। এই কেস আমি ভাল করে দেব।”
শশিতারার বুক থেকে ভার নেমে গেল। বলবেন, “বড় অশান্তিতে আছি। ভেবে ভেবে মানুষটা শুকিয়ে গেল। মুখে কিছু তুলতেই চায় না। আপনি যা পারেন করুন।”
খানিকটা পরে গুরুপদ এলেন। সঙ্গে জুনিয়ার, মানে মুরলী।
গুরুপদ এমনভাবে এলেন যেন মুখ থুবড়ে পড়ে গিয়েছিলেন কোথাও। চোট খেয়েছেন। হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছিল।
মহাদেব মুরলীকে বললেন, “সব ঠিক করে দিয়েছ?”
“হ্যাঁ।”
“বসুন।” মহাদেব গুরুপদকে বসতে বললেন, “প্রথম প্রথম একটু অসুবিধে হবে। পরে সয়ে যাবে।”
গুরুপদ বললেন, “লোহার খোঁচা লাগছে।”
“প্রথমটায় লাগে।—তা আপনি তো দেখলেন কীভাবে দিয়ে দেওয়া হয়েছে টুকরোগুলো। ঠিক এইভাবে সকালে দু ঘন্টা দুপুরে দু ঘণ্টা রাত্রে এক ঘণ্টা। শোবার সময় সব খুলে রাখবেন। শোবেন উত্তর দক্ষিণ মাথা করে। যদি পারেন বিছানায় ম্যাগনেটগুলোকে রেখে দেবেন। প্লাস দাগগুলো মাথার দিকে, মাইনাসগুলো পায়ের দিকে।”
শশিতারা উসখুশ করছিলেন। আর পারলেন না। স্বামীকে বললেন, “ডাক্তারবাবু তোমায় চেনেন। স্কুলের বন্ধু।”
গুরুপদ মহাদেবকে দেখতে লাগলেন।
মহাদেব বললেন, “স্কটিশ স্কুল!”
“হ্যাঁ—তা—”
“আপনি আমার সিনিয়ার ছিলেন। স্কুলে আপনাকে সকলে গুরু বলে ডাকত। আর আমাকে বলত, মানে আমার ডাকনাম ছিল, ঝন্টু।”
গুরুপদ যেন চমক খেয়ে গেলেন। “ঝনু ঝন্টু যে স্কুলের মধ্যে খেপা ষাঁড় ঢুকিয়ে দিয়েছিলে?”
মহাদেব হাসতে হাসতে বললেন, “নাম আমার মহাদেব। ষাঁড় আমার বাহন। “
গুরুপদ হেসে উঠতে গিয়ে বুকে খোঁচা খেলেন। সামলে নিয়ে বললেন “তুমি আমায় অবাক করলে ঝন্টু! শুনেছিলাম তুমি নেভিতে গিয়েছ। তা এ তো অন্য ব্যাপার। তোমার এই ম্যাগনেট ডাক্তারি কবে থেকে?
“অনেক দিন হল। কলকাতায় এসেছি বছর দুই। এখনও জমাতে পারিনি তেমন। দিল্লি চণ্ডিগড়ে ভাল জমিয়েছিলাম।—শেষে আর ভাল লাগল না। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে এলাম। ভাইপোটাকে তো মানুষ করে দিয়ে যেতে হবে।”
শশিতারা মুরলীর দিকে তাকিয়ে বললেন, “আপনার ভাইপো ছেলেটি বেশ।”
শানু একবার শশিতারাকে দেখে নিল।
ছয়
মাস খানেক পরের কথা। চৈত্রমাসের শেষ। গরমে কলকাতা পুড়ে যাচ্ছে। বৈশাখে বুঝি ঝলসাবে।
গুরুপদ গলদঘর্ম হয়ে সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে ডাকলেন।
শশিতারার সারা দিনে বার চারেক স্নান আর গা-ধোওয়া হয়েছে। সবে গা ধুয়ে শাড়ি পাল্টাচ্ছিলেন। সাড়া দিয়ে বললেন, “আসি।”।
শশিতারা ঘরে আসতেই গুরুপদ বললেন, “সুবোধের কাছে গিয়েছিলাম।”
“কী বলল?”
“দেখল। বলল, ভেরি গুড। এই রেটে ঝরে যাও।” গুরুপদ একেবারে নগ্নগাত্র হয়ে গায়ের ঘাম শুকোচ্ছিলেন। “আরও ছ মাস ঝরতে হবে।”
শশিতারা বললেন, “কেন, তুমি কি খেজুর গাছ। কলসি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখলে রস ঝরবে!”
গুরুপদ বললেন, “আমি বললাম, আরও ছ মাস ঝরব। বলো কী! তা ও বলল, শীতের পাতা ঝরা দেখে ভয় পেও না। শীতের পরই বসন্ত। তখন নবপল্লব।”
“যত্ত বাজে কথা! আর ঝরাঝরিতে কাজ নেই। “।
“মাস খানেক বাইরে গিয়ে বেড়িয়ে আসতে বলল। ফাঁকা জায়গায়। বলল, বাইরে গিয়ে মাঠেঘাটে মাইল দু তিন করে হাঁটবে রোজ। “
“বেশ কথা। মাঠে মাঠে গোরু চরে, মানুষ নয়। ”
“আমি বললুম, বৈশাখ মাসে একবার না হয় চেষ্টা করব। পুরী যেতে পারি।”
“সে বরং ভাল। সমুদ্র ভাল।”
“অনেক দিন বাইরে বেরুনো হচ্ছে না। পুরীই ভাল। কার্তিকবাবুর বাড়িটা নিয়ে নিলেই হবে। সবাই মিলে ঘুরে আসব। ”
“হবেখন। পুরীতে বাড়ি পেতে আটকাবে না। আমাদের ছোড়দার বাড়ি আছে।—ওদের লোকজন থাকে। ব্যবস্থা করা রয়েছে।—নাও তুমি সেরে নাও। তোমার মুরলী এসে বসে আছে!”
“ম্যাগনেট মুরলী!” স্ত্রীকে একবার দেখলেন গুরুপদ।
“বেলুর সঙ্গে বসে গল্প করছে।”
“শানু নেই?”
“এখনও ফেরেনি।”
“আমি চানটা সেরে আসছি।”
মুরলীর নাম হয়েছে এ-বাড়িতে ম্যাগনেট মুরলী। শানুই চালু করেছিল। এখন অন্যদের মুখে মুখে ঘুরছে।
শশিতারা বললেন, “চান করে তুমি দোতলায় নামবে? না—?”
“নীচেই নামব।”
“আজ দুটো ডায়াবিটিস সন্দেশ খাও। মুরলী হাতে করে এনেছে।”
“সন্দেশও আনছে নাকি মুরলী আজকাল! বাঃ বাঃ!”
শশিতারা চলে গেলেন।
গুরুপদও আর বসে থাকলেন না বৃথা। স্নান করতে বাথরুমের দিকে পা বাড়ালেন।
দোতলার বসার ঘরে মুরলী বসে বসে গল্প করছিল। এক পাশে মুরলী, মুখোমুখি সোফায় বসে বেলা।
মুরলী ছেলেটিকে প্রথম দিন যতটা মুখচোরা মনে হয়েছিল, ততটা মুখচোরা সে নয়। তবে খুব যে সপ্রতিভ তাও নয়। হাসি-খুশি মুখ। কথা বলে নরম গলায়।
স্নান সেরে গুরুপদ নীচে নামলেন।
“এই যে জুনিয়ার!” গুরুপদ ঘরে ঢুকে ঠাট্টা করে বললেন, “এসেছ কখন? কাকার খবর কী?”
মুরলী উঠে দাঁড়িয়েছিল। বলল, “এসেছি খানিকক্ষণ। কাকা ভালই আছে।”
“বসো বসো।—আমার ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম।”
“কী বললেন?”
“ভালই বলল। বলল, আরও ঝরতে হবে। লাইক এ উইনটার ট্রি।” বলতে বলতে গুরুপদ নিজে সোফায় বসলেন। “ব্যাপারটা কী জান, আমি নিজে আজকাল মন্দ বুঝছি না।” বেলা উঠি উঠি ছিল। গুরুপদর সেদিকে নজর পড়তেই হাত তুলে ইশারায় বেলাকে বসতে বললেন।
মুরলী বলল, “খারাপ হবার কথা নয়। ইন ফ্যাক্ট আপনাকে যে কটা পিস ম্যাগনেট দিয়েছিলাম লাস্ট টাইম—তার টোটাল ওয়েট সাতশো থেকে সাড়ে সাতশো গ্রাম। এক কেজি মতন দিলে ঠিক হত। কাকা বলল, খানিকটা কম দিয়েই দেখা যাক।”
গুরুপদ বললেন, “আমি কিন্তু বাবা ডাক্তারের কাছে যাবার সময় গা থেকে খুলে গাড়িতে রেখে গিয়েছিলাম।” বলে একটু হাসলেন।
“ভাল করেছিলেন” মুরলী বলল, ‘কুকুর বেড়ালে মিশ খায় না। যারা ট্রাডিশনাল ডাক্তার তারা আমাদের ব্যাপারটা মানতে চায় না। শুনলে চটে যায়। আপনার বন্ধুর সঙ্গে অনর্থক কেন চটাচটি করবেন!”
এমন সময় শশিতারা নিজেই কর্তার জন্যে ডায়াবেটিস সন্দেশ, আর ঘোলের শরবত নিয়ে হাজির। শরবতে চিনির নামগন্ধও নেই, নুন আছে।
স্বামীর কাছেই একটা টিপয় ছিল। সন্দেশ শরবত নামিয়ে রাখলেন।
মুরলী বলল, “ম্যাগনেটগুলো আবার পরেছেন?”
“না। চানটান সেরে এলাম। পরে পরব।”।
মুরলী বলল, “ওগুলো আর পরবেন না। আমি নতুন সেট এনেছি।” এমনভাবে বলল কথাটা যেন নতুন সেট গয়না এনেছে।
গুরুপদ বললেন, “নতুন সেট?”
“হ্যাঁ,” বলে পাশে রাখা প্লাস্টিকের ছোট বাক্স দেখাল মুরলী।
শশিতারা স্বামীকে তাড়া দিলেন, “তুমি খেয়ে নাও। “
গুরুপদ সন্দেশের দিকে হাত বাড়ালেন।
মুরলী বলল, “ছটা। দুটো হার্টের জন্যে। একশো গ্রাম মতন। ফিফটি ফিফটি গ্রামস। দুটো থাকবে কোমরে। এদের ওয়েট একশো গ্রাম ইচ! এই হল তিনশো। আর লেগ-ম্যাগনেট একশো টোটাল-ওয়েট এবার চারশো। “
বেলা বলল, “অর্ধেক হয়ে গেল যে আগের চেয়ে।”
“জাস্ট ফর এ উইক। পুরনোগুলো আবার ম্যাগনেটাইজ করে পাওয়ার বাড়াতে হবে। বডিতে থাকতে থাকতে উইক হয়ে গিয়েছে।”
গুরুপদ বললেন, “মানে বড়ি কনট্যাক্টে?”
মুরলী বলল, “হ্যাঁ। আমরা রিচার্জ করে স্ট্রেংথটা বাড়িয়ে দি। মাঝে মাঝে স্ট্রেংথ কমবেশি করে দেখি রোগীর পক্ষে কোনটা স্যুটেবল হচ্ছে।” বলে গুরুপদর দিকে তাকাল, বলল, “আমাদের একটা বড় অসুবিধে কি জানেন, ডাক্তারদের মতন আমরা ওষুধের শিশির গায়ে লেখা স্পেসিফিক ডোজ দেখে কাজ করি না। আমাদের হল অবজারভেশান, আন্দাজ, এক্সপেরিমেন্ট।—এই যে আপনাকে নতুন সেটটা যা দেব—তার টোটাল ওয়েট কম। ম্যাগনেটিক স্ট্রেংথও কম। কিন্তু দিয়ে দেখব, কী রেজাল্ট হয়। এটা একটা ব্রেক—!”
গুরুপদ বললেন, “আচ্ছা মুরলী, হরিনামের মালার থলির মতন একটা মশারির থলি করে যদি বুকের কাছের ম্যাগনেটগুলো ঝুলিয়ে রাখি, হয় না? —তুমি যাই বলো, পট্টি দিয়ে ওই লোহার টুকরো বুকে বেঁধে রাখতে কষ্ট হয়। খচখচ করে লাগে।—গরম কাল। একেই তো আমার ঘামের ধাত।”
বেলা হেসে ফেলল। মুরলী মাথা নাড়ল। বলল, “না জেঠু ; বডির সঙ্গে যত বেশি কনট্যাক্ট হবে তত কাজ হবে।”
গুরুপদ কিছু বললেন না। হাঁটুর কাছে চুম্বক দুটো পট্টি দিয়ে বেঁধে নিকাপ পরে চালাচ্ছেন তিনি, কোমরের কাছেও চুম্বক রেখে পট্টি বাঁধছিলেন। অসুবিধে অস্বস্তি দুইই হচ্ছে। তবে বুকের পট্টিটাই সবচেয়ে কষ্ট দিচ্ছিল তাঁকে।
বেলা আড়চোখে চাইল। বলল, “হেড ফোনের মতন একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারলে ভাল হয় না?”
মুরলী বলল, “ভেবে দেখব। বলে গুরুপদকে বলল, “ম্যাগনেটের পোলগুলোকে ঠিক মতন রাখছেন তো! দাগ তো দেওয়াই আছে। শোবার সময় নর্থ সাউথ হয়ে শোবেন। বসার সময়ও যতক্ষণ পারবেন—”
শশিতারা বললেন, “আমার বাতের জন্যে এক জোড়া দিও তো। আমি কিন্তু বাঁধাবাঁধি করতে পারব না!”
মুরলী যেন কিছু ভাবল। তারপর বলল, “আপনাকে কীভাবে দেওয়া যায় ভেবে দেখব।—তবে আপনি উপকার পাবেন। বাত, স্পণ্ডিলাইটিস—এসব রোগে ম্যাগনেট ট্রিটমেন্ট ভীষণ কাজে দেয়।”
“অ্যাকুপাংচারের চেয়েও বেশি?” গুরুপদ বললেন।
“অনেক বেশি। অ্যাকুর হল নারভাস সিস্টেমের কতকগুলো ভাইট্যাল পয়েন্ট নিয়ে কাজ। ম্যাগনেটের হল পুরো শরীর নিয়ে। এটা কাজ করছে ইউনিভারসাল ম্যাগনেটিক এফেক্ট নিয়ে।”
“ও ! ইউনিভারসাল—!” গুরুপদ প্রথম সন্দেশ শেষ করে দ্বিতীয় সন্দেশ মুখে পুরলেন। “কোথাকার সন্দেশ হে?”
“নিউ সুইটস-এর।—শিয়ালদার কাছে।”
“মন্দ নয়। তবে একটু গন্ধ আছে।”
“আজ্ঞে চিনি থাকলে গন্ধটা লাগত না।—সন্দেশে একটু ফ্লেভার নেই?”
“বুঝতে পারছি না। যাক গে, আগের বারে কী একটা এনেছিলে?”
“চিনি ছাড়া রসগোল্লা!”
“তাই হবে!” বলে শশিতারার দিকে তাকালেন গুরুপদ, “দিনে দিনে কী হচ্ছে দেখছ তো! চিনি ছাড়া সন্দেশ রসগোল্লা, ফল ছাড়া ফলের রস, তা ছাড়া ডিম। আরও কত হবে দিনে দিনে। এই যেমন দেখছি—ম্যাগনেট ট্রিটমেন্ট—।”
মুরলী তার ঘড়িটা দেখে নিল। বলল, “এবার আমি উঠব। পুরনো ম্যাগনেটগুলো নিয়ে যেতাম।”
শশিতারা বেলাকে বললেন, “যা তোর মামার ঘর থেকে ওগুলো নিয়ে আয়।”
বেলা উঠতে যাচ্ছিল, গুরুপদ বললেন, “ওপরে কি পাবে?”
“কোথায় রেখেছ তবে?”
“মনে করতে পারছি না। সুবোধের কাছে যাবার সময় গাড়িতে খুলে রেখেছিলাম।”
“গাড়ি তো গ্যারেজে।”
“দেখতে হবে।”
“বেলি, দেখ কোথায় রেখেছে। গাড়িতে থাকলে দুলালকে বলবি, গ্যারেজ খুলে গাড়িটা দেখতে।”
বেলা চলে গেল।
গুরুপদ মুরলীকে বললেন, “তোমাদের এই ম্যাগনেট ট্রিটমেন্টটা কোথায় শিখেছিলে? দিল্লিতে?”
“আজ্ঞে হ্যা। ডক্টর ভার্গবের কাছে। উনি জার্মানি থেকে ফিরে এসে ব্যাপারটা শুরু করেন। বম্বেতে শুরু করেন ডক্টর দেশপাণ্ডে। অনেক পরে। কাকা ভার্গবের সঙ্গে কাজ করতেন। আমাদের দেখে আপনি ডক্টর ভার্গরে ব্যাপারে কিছু বুঝবেন না।ওঁর ক্লিনিক দেখার মতন জিনিস। কত রকম ব্যবস্থা, যন্ত্রপাতি—! আমরা কিছুই করে উঠতে পারিনি। কাকার ইচ্ছে অনেক ; কিন্তু অত টাকা পয়সা আমাদের নেই।”
ঘোলের শরবতে চুমুক দিতে দিতে গুরুপদ বললেন, “হবে, তোমাদেরও হবে।”
শশিতারা ইশারায় গুরুপদকে দেখালেন ; দেখিয়ে বললেন, “উনি কত ছোট থেকে শুরু করেছিলেন। সকাল রাত দিন দুপুর খেটে খেটে মরেছেন। তবে না আজ—”
গুরুপদ কথা শেষ করতে না দিয়ে বললেন, “বাড়ি, গাড়ি, কারখানা—। সবই ওঁর বরাতে হে।—তা মুরলী, তোমার কাকা না হয় ছেলেবেলা থেকে স্কুলে ষাঁড় ঢুকিয়েছে। তুমি বাপু কাকার লাইন ধরলে কেন?”
মুরলী যেন কথাটা বুঝতে পারল না। আমতা আমতা করে বলল, “আজ্ঞে, কাকাই আমার সব। কাকাই আমায় মানুষ করেছে। বাবা নেই, মা নেই। তা ছাড়া আমি ফিজিওলজি নিয়ে পড়াশোনা করেছি।”
“ও! —বুদ্ধিমান ছেলে!” গুরুপদ ঘোল শেষ করে সেঁকুর তুললেন। দরজার দিকে তাকালেন একটু। “কই, গেল তো গেলই, আর এল না।”
মুরলী বলল, “আমি তো নীচেই যাচ্ছি। নিয়ে নেব।—নতুন সেটটা রেখে গেলাম।”
প্লাস্টিকের বাক্সটা রেখে দিয়ে উঠে পড়ল মুরলী। “আসি। খবর নিয়ে যাব।”
মুরলী চলে গেল।
গুরুপদ দুটি চোখ বন্ধ করে সামান্য বসে থাকলেন। তারপর নিজের মনেই বললেন, “ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখোনি।”
শশিতারা কিছু বুঝতে পারলেন না। “কী হয়েছে?”
“না; তেমন কিছু নয়।— চলো, ওপরে যাই।”
গুরুপদ সোফা থেকে উঠে পড়লেন। শশিতারা বললেন, “তোমার কি এত ওপর নীচ পোষায়! নামলে যখন তখন দু দণ্ড বসলেই পারতে।”
“একটা ফোন করব।”
“কাকে?”
“চলো, দেখবে।”
শশিতারাকেও উঠতে হল।
দরজার দিকে পা বাড়িয়ে শশিতারার মনে হল চুম্বকের টুকরো রাখা প্লাস্টিকের বাক্সটা পড়ে রয়েছে। তুলে নিতে গেলেন।
গুরুপদ বললেন, “ওটা থাক।”
“কেন? পরবে না?”
“না।— এসো।”
শশিতারা কিছুই বুঝলেন না। অবাক হলেন। হয়েও কিছু বললেন না। পাখা বন্ধ করে দিলেন। দিয়ে স্বামীর পিছু পিছু সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন।
তেতলায় এসে গুরুপদ শোবার ঘরে না ঢুকে পাশের ঘরে ঢুকলেন। ডাকলেন স্ত্রীকে।
“একটা ফোন করব।”
“কাকে?”
“মহাদেবকে। বাড়িতেই পাব এখন। দেখি।”
গুরুপদ একটা সরু খাতা হাতড়ে মহাদেবের ফোনের নম্বরটা দেখে নিলেন। নম্বরটা হালে টোকা হয়েছে।
শশিতারা পাখাটা চালিয়ে দিলেন ঘরের।
গুরুপদ বার পাঁচেক চেষ্টা করে মহাদেবকে পেলেন।
“মহাদেব নাকি? আমি গুরুপদ বলছি।” —গুরুপদ ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, “—না না, ভালই আছি।— সুবোধ ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম।— বলল, বেটার।— বাড়ি ফিরে এসে দেখি, তোমার জুনিয়ার বসে আছে।—হ্যাঁ গো, তোমার ম্যাগনেট মুরলী।— কী।—তা তুমি অমন জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলছ কেন? মালটাল খেয়েছ নাকি! —যাক গে শোননা। তুমি তো স্কুলে ষাঁড় ঢোকানো ছেলে! তা আমার পেছনে এবার যে ম্যাগনেটটি ঢুকিয়েছ তার কী হবে! —কী বলছে, বুঝতে পারছ না! মহাদেব—আমাকে তুমি বুদ্ধু ভেবেছ। শোনো, তোমার ওই ভাইপো মুরলী, আর আমার ভাগ্নি বেলা—এই ছোঁড়াছুঁড়ি দুটোর আগে থেকেই চেনাজানা হয়েছে।—আরে বাবা, তুমি আমায় কী শেখাবে! আমি শিখে শিখে বুড়ো হয়ে গেলুম।—দাঁড়াও, দাঁড়াও—আমাকে কথা শেষ করতে দাও—কলকাঠি তুমি নাড়োনি জানি। নেড়েছে আমার ভাগ্নি আর শালীর ছেলে। হারামজাদা কেমন প্যাঁচ কষে আমাকে, আমার গিন্নিকে তোমার কাছে নিয়ে গেছে বুঝতে পারছি। তুমিও বাপু, বেশ ম্যাগনেটটি ঢুকিয়ে দিলে। ”
শশিতারা যতই অবাক হচ্ছিলেন ততই স্বামীর গা ঘেঁসে আসছিলেন। যেন পারলে মহাদেবের কথাগুলোও শুনে নেন।
গুরুপদ বললেন, “—শানু—আমার শালীর ছেলেটি অতি ধুরন্ধর। ভাগ্নিটাকে আমি বোকাই ভাবতাম।—দেখছি, এখনকার ছেলেমেয়েগুলো আমাদের কান কাটতে পারে।—তা যাকগে এখন তোমায় সাফসুফ বলি, তোমার ভাইপোকে আমার জামাই করতে পারছি না। ছোকরাকে বলে দিও!” বলে গুরুপদ ফোন নামিয়ে রাখলেন।
শশিতারা অবাক হয়ে স্বামীকে দেখছিলেন। প্রথমে কথা বলতে পারছিলেন না পরে বললেন, “হল কী তোমার?”
“আমার সঙ্গে ভাঁওতা বাজি।”
“করলটা কে?”
“ওরা!—আমি বলব না করে শেষে সুবোধকে বলেই ফেললাম, ম্যাগনেটিক ট্রিটমেন্টের কথা। সুবোধ তো হাসতে হাসতে বিষম খেয়ে মরে। শেষে বলল, আমার মতন ছাগল আর দেখেনি।”
“তোমায় ছাগল বলল! ও নিজে কী?”
“ও কী তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।—সত্যি বলতে কি, আমি ফেরার সময় গাড়িতে ভাবতে ভাবতে এসেছি।—আমার বরাবরই কেমন ধোঁকা লাগছিল। চার ছটা লোহার টুকরো বেঁধে চিকিৎসা! —তা কলকাতা শহরে হাজার লোক হাজার ফিকির করে খায়! তোরাও খা। নো অবজেকশান। আমিও শালা আদি আমলা তেল, চালমুগরা করে খাই।—কিন্তু তোরা আমার ভাগ্নিকে চিট করবি?”
শশিতারা হঠাৎ বললেন, “মুরলী ছেলেটি কিন্তু ভাল। দেখতে ভাল ব্যবহার ভাল। লেখাপড়া শিখেছে। সভ্য—”।
“সভ্য! —বেটাকে তুমি সভ্য বলছ! —তুমি কিস্যু জানো না।—শোনো, তোমায় বলিনি আজ আমি যখন ওপরে আসছি, কানে এল বসার ঘরে বসে ওই রাস্কেল হি হি করে হেসে হেসে বেলিকে বলছে, বেলা তোমার কাছে এইভাবে বসে থাকলে আমার মনে হয় ময়রার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। জিবে জল আসে।”
শশিতারা হেসে ফেললেন। জোরেই। তাঁর মোটা গলার স্বর সরু হয়ে এল।
গুরুপদ বললেন, “হাসছ।”
শশিতারার হাসি আর থামতে চায় না। শেষে বললেন, “সে তুমি বলতে। তুমি ময়রার দোকান বলতে না, বলতে—”।
গুরুপদর মনে পড়ে গেল, কী বলতেন। নানা রকমই বলতেন, মাঝে মাঝে তামাশা করে বলেছেন, শশিসোনার ভ্যারাইটি স্টোর্স—।
হেসে ফেলে গুরুপদ বললেন, “সে তখনকার কথা। বিয়ের পর। বিয়ের আগে অমি তোমায় দেখেছি, না, কিছু বলেছি?”
শশিতারা বললেন, “দেখোনি বলোনি।—এরা দেখাদেখি করছে তাই বলছে।”
এমন সময় বেলার গলা পাওয়া গেল। ঘরে এল। এসে বলল, “গাড়িতে কিছু নেই। “বেলার হাতে বসার ঘরে ফেলে আসা প্লাস্টিকের বাক্স।
গুরুপদ ভাগ্নিকে দেখতে দেখতে বললেন, “নেই জানতে এতক্ষণ লাগল?”
বেলা চুপ। মুখ নিচু করল।
শশিতারা বললেন, “তোর মামার খেয়াল থাকে না কোথায় ফেলে দিয়েছে।”
বেলা নতুন বাক্সটা এগিয়ে দিচ্ছিল, গুরুপদ বললেন, “আমার দরকার নেই। তুমি নিয়ে যাও।”
বেলা হকচকিয়ে গেল। “আমি?”
শশিতারা ইশারা করে বললেন, “তুই নিয়ে যা। যা—!”
বেলা যেন কেমন থতমত খেয়ে ভয় পেয়ে চলে গেল।
গুরুপদ গোঁফ চুলকোতে চুলকোতে বললেন, “শশি? কী করব?”
“আর একবার ফোন করো।”
“কাকে?”
“মহাদেবকে?”
“কী বলব?”
“বলো, যা হয়েছে ; তাই হবে।”
“শুধু এই?”
“হ্যাঁ।—তুমি তো খাঁটি দিশি ছেলে খুঁজছিলে। মুরলী তোমায় ম্যাগনেট দেওয়া চুলের তেলও করে দিতে পারে।”
গুরুপদ আবার ফোন করলেন।
“মহাদেব।—আমি গুরুপদ।—শোনো, আমার বউ বলছে—যা হচ্ছিল, তাই হবে।—কী? শুনে খুশি হলে।—আরে—কী বললে ম্যাগনেট ট্রিটমেন্ট! না আমার দরকার নেই। ওটা যাদের দরকার তারাই করুক।—কী? —কী বলছ? —তা বলতে পার। ছাড়লাম।”
গুরুপদ ফোন নামিয়ে রাখলেন।
শশিতারা বললেন, “কী বলল গো মহাদেব?”
“বলল, বউদিই তোমার বেস্ট ম্যাগনেট! —শালা ধড়িবাজ।” বলে গুরুপদ বেশ হাসিখুশি মেজাজে শশিতারার বুকে খোঁচা মারলেন। “ম্যাগনেট! মন্দ বলেনি, কী বলো? তবে এত বিগ সাইজ—!”
শশিতারা বুক সামলে বললেন, “আঙুল না ছাতার বাঁট! আমার লাগে না?”
গুরুপদ হাসতে লাগলেন।
প্রেমশশী
বিয়ের পর পনেরোটা দিনও কাটেনি প্রেমকিশোর বন্ধুদের কাছে এসে কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, ভাই, তোরা আমায় ত্রিশূল পর্বতের একটা টিকিট কেটে দে, আমি পাহাড়ে চলে যাব।
ত্রিশূল পর্বতটা কোথায় বন্ধুদের কারও জানা ছিল না। গুহ জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ায় কাজ করে, ভারতবর্ষের মানচিত্রটা তার মোটামুটি জানা—সেই গুহও বলল, একজ্যাক্ট লোকেশানটা কোথায় ত্রিশূলের?
প্রেমকিশোর বিরক্তির চোখে গুহর দিকে তাকাল।
সুবীর হাজরা আর মন্মথ প্রেমকিশোরকে ভাল করে নজর করতে লাগল। পনেরো দিনেই প্রেমকিশোর রং-ওঠা জামার মতন মেড়মেড়ে মেরে গেছে, তার মুখে জেল্লা নেই, মাথার চুলে হেয়ার-ক্রিমের পালিশ নেই, গাল-টাল শুকনো, চোখ গর্তে ঢুকেছে। দেখলে মনে হচ্ছে, ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি থেকে সদ্য উঠে এসেছে।
সুবীর হাজরা জীবনের নানা ব্যাপারে অভিজ্ঞ। প্রেমকিশোরের প্রায়-বিধ্বস্ত চেহারা খুঁটিয়ে নজর করতে করতে বলল, “বুঝেছি দি সেম প্রবলেম। আমাদের বঙ্কিমের মতন। ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলি বুঝি?” বলে সুবীর একটু টেরচা চোখে হাসল।
মন্মথ বলল, “আমরা তো জানতাম তুই বউ নিয়ে হনিমুন করে বেড়াচ্ছিস। পুরী যাবি বলেছিলি না?”
প্রেমকিশোর বুক ভাঙা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, “হনিমুন কোথায় ভাই, আমার হনি গন, —আর মুন ভ্যানিশ হয়ে গেছে।”
গুহ ভড়কে গিয়ে বলল, “হনি গন মানে কি রে? বউ পালিয়ে গেছে নাকি?” প্রেমকিশোর বলল, “না, বউ পালায়নি। আমি পালাব। ।’’
সুবীর বলল, “কি আজেবাজে কথা বলছিস! তুই পালাবি কেন? কী হয়েছে তোর! বিয়ের পর প্রথম প্রথম ছেলেদের ও-রকম একটু হয়। ওটা নার্ভাসনেসের ব্যাপার। মালটি-ভিটামিন খা, আর দুটো আসন কর, ঠিক হয়ে যাবে।”
প্রেমকিশোর প্রবলভাবে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল; “না না, তা নয় ; বঙ্কিমের কেস না। সে-কেস অনেক ভাল ছিল। আমার কেস কোয়াইট ডিফারেন্ট। আমি আর বাঁচব না।”
মন্মথ বন্ধুর অবস্থা দেখে বলল, “তুই অত কাহিল হয়ে পড়ছিস কেন। ব্যাপারটা কী খুলে বলবি তো! আমরা এতগুলো ম্যারেড লোক রয়েছি; সিজন্ড, তোর প্রবলেম সল্ভ করতে পারব না? আলবাত পারব। কী হয়েছে বল?”
গুহ বলল, “তুই একটু জল খেয়ে নে প্রেম, সুস্থ হয়ে নে। শুধু জল খাবি, না জলবৎ ব্র্যান্ডি খাবি? দুই তোকে খাওয়াতে পারি।” বলে গুহ হাসল।
প্রেমকিশোর অভিমান করে বলল, “আমায় কিছু খাওয়াতে হবে না ভাই, নিমতলায় যাবার পর দু ফোঁটা গঙ্গার জল দিস, তা হলেই হবে।”
মন্মথ জিভ কেটে বলল, “ছি ছি, বলছিস কি! এখন তুই ম্যারেড, সবেই লাইফ শুরু করেছিস,…কত সুখ আহ্লাদ পড়ে আছে জীবনে।”
বুকে হাত রেখে প্রেমকিশোর বলল, “আমার জীবনে আর কিছু নেই। এখন একটা খাঁচায় পোরা বাঁদর বনে গিয়েছি।”
সুবীর বলল, “বাজে বকিস না। তোর মাথায় শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে। সব ঠিক করে দেব। এই গুহ, চা বলে আয় ভেতরে।”
গুহ বাড়ির মধ্যে চায়ের কথা বলতে গেল।
প্রেমকিশোরের বিয়ের একটা ইতিহাস আছে। তার বন্ধু—বান্ধবরা আটাশ ত্রিশ বড় জোর বত্রিশের মধ্যে বিয়ে করে ফেললেও প্রেমকিশোর সাঁইত্রিশ বছর বয়েস পর্যন্ত অনড় অটল থেকে গেল। তার কারণ প্রেমকিশোরের বাল্যকাল থেকেই কেমন একটা প্রেম-প্রেম বাতিক হয়েছিল। তার বাল্যসঙ্গিনী ছিল পাশের বাড়ির লাবণ্য—ডাক নাম লাবু। প্রেমকিশোর সেভেন ক্লাসে পড়ার সময় সাপ-লুডো খেলতে খেলতে একদিন লাবুকে মনোচোর বলেছিল ; তার ফলে লাবু প্রেমকিশোরের হাতে এমন কামড় কামড়েছিল যে বেচারি প্রেমকিশোরকে এ টি এস নিতে হয়েছিল। ‘মনোচোর’ শব্দটা প্রেমকিশোর নজরুলের গানে শুনেছিল। মানেটা বোঝেনি। যাই হোক, বাল্যপ্রেমে এই ভাবে বিচ্ছেদ ঘটে। কৈশোরে প্রেমকিশোর তার এক পিসির ভাশুরঝির প্রেমে পড়ে। সেই মেয়েটির নাম ছিল হাসি। হাসি যত না হাসত তার চেয়ে বেশি কাঁদত। একবার শিয়ালদায় রথের মেলায় প্রেমকিশোর হাসিকে নিয়ে রথ দেখতে গিয়েছিল। রথ দেখতে গিয়ে সে তার কিশোরী প্রেমিকা হাসিকে এত বেশি তেলেভাজা খাইয়েছিল যে হাসি পেটের ব্যথায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে ডাক ছেড়ে কাঁদতে শুরু করে। তার কান্না শুনে লোকজন ভিড় করতে থাকল, শেষে পুলিশ এসে দাঁড়াল। হাসি রাস্তায় উবু হয়ে বসে বমি করে অনবরত, আর আঙুল দিয়ে প্রেমকিশোরকে দেখায়, বলে, ওই ছেলেটা—ওই ছেলেটা—। যাই হোক, প্রেমকিশোর খুব বেঁচে গিয়েছিল। কলেরা হতে হতে হাসিও বেঁচে গেল। কিশোর প্রেমটাও রথের মেলায় ভেঙে গেল প্রেমকিশোরের। তারপর যৌবনে প্রেমকিশোর বার তিনেক নিজেকে লটকে ফেলার চেষ্টা করেছে, একবার বেণুর সঙ্গে ; পরের বার সুরূপার সঙ্গে ; আর শেষ বার আইভির সঙ্গে। বেণুর বাবা প্রেমকিশোরের পিছনে তাঁদের বিশাল অ্যালসেশিয়ানকে লাগিয়ে দিয়েছিলেন, ফলে প্রেমকিশোর বেণুদের বাড়িতে ঢুকতেই পারল না। সুরূপার বেলায় প্রেমকিশোর একদিন ট্যাক্সি করে হাওয়া খেতে বেরিয়েছিল সুরূপাকে নিয়ে। সন্ধেবেলায় রেড রোডে গাড়ি গেল খারাপ হয়ে, অ্যাক্সেল গেল ভেঙে। ড্রাইভার বলল, বাবু তোমরা একটু গাড়িটা দেখো। আমি মিস্ত্রি ডেকে আনছি। ডাইভার গেল তো গেল, আর আসে না। প্রথম প্রথম প্রেমকিশোরের ভালই লাগছিল—এমন নির্জনে নিরিবিলিতে সুরূপাকে পাওয়া ভাগ্যের কথা। একটু চঞ্চল হয়ে সুরূপাকে প্রেম-ট্রেমের কথা বলতে গিয়েই ধাক্কা খেল প্রেমকিশোর। সুরূপা বলল, এ সমস্ত তোমার চালাকি! তুমি ড্রাইভারের সঙ্গে সাঁট করেছ। ছোটলোক, অসভ্য, ইতর। দাঁড়াও না, পুলিশের গাড়ি এবার এলেই আমি হাত দেখাব। তোমায় আমি দেখাচ্ছি।…
সুরূপার হাতে পায়ে ধরে প্রেমকিশোর বাঁচল। একটা প্রাইভেট গাড়ি থামিয়ে চলে গেল সুরূপা; আর প্রেমকিশোর ট্যাক্সির মধ্যে ভূতের মতন বসে থাকল। ঘণ্টা দুই পরে ট্যাক্সিঅলা ফিরল, বলল, আমার সর্বনাশ হল বাবু, আপকো তো মজা হল, থোড়া জাদা টাকা ছাড়ন, পঁচাশ…। প্রেমকিশোর নাক কান মলে পালাল। শেষে এল আইভি। নাচ জানত। প্রেমকিশোরকে মাস কয়েক বেশ নাচাল, তারপর একদিন প্রেমকিশোরকে দিয়েই বম্বের একটা ফার্স্ট ক্লাস টিকিট কাটিয়ে বম্বে চলে গেল ফিল্মে চান্স খুঁজতে।
প্রথম থেকে পর পর এতগুলো ধাক্কা খাবার পর প্রেমকিশোর নারী—বিদ্বেষী হয়ে উঠল। প্রতিজ্ঞা করল, বিয়ে করবে না। মা যতদিন বেঁচে ছিল বিয়ে বিয়ে করত, মা মারা যাবার পর সেদিক থেকেও নিশ্চিন্ত। বাবা আগেই গিয়েছেন। নিজের বলতে আর কেউ নেই। ছোট বোন বিয়ের পর মাদ্রাজে থাকে। আসেও না। নির্ঝঞ্ঝাটে ছিল প্রেমকিশোর; বাপের আমলের ছোট্ট বাড়ি, আর বেসরকারি অফিসে চাকরি—চমৎকার ছিল।
বন্ধুবান্ধবদের বিয়ে হয়ে যেতে লাগল, বিয়ের পর বাচ্চাকাচ্চা; তাদের নাস্তানাবুদ অবস্থা দেখত প্রেমকিশোর আর হাসত, বলত, নে এবার ঠেলা বোঝ ; আমি আমার লর্ড হয়ে আছি। বন্ধুরা প্রেমকিশোরকে বিয়ের উপকারিতা সম্বন্ধে বোঝাত, জ্ঞান দিত, ফুঁসলাবার চেষ্টা করত। প্রেমকিশোর বলত, তোমরা লেজ কেটেছ, বেশ করেছ, আমি লেজ কাটছি না, ভাই।
গত বছর প্রেমকিশোর হুট করে এক বড় অসুখে পড়ল। ভুগল মাসখানেক। বন্ধুবান্ধব তাদের স্ত্রীরা প্রেমকিশোরের দেখাশোনা করল। বাড়ির চাকরটা কত আর পারবে। অসুখ থেকে উঠে প্রেমকিশোরের মনোভাব খানিকটা পালটে গেল। বছর সাঁইত্রিশ বয়েস হয়ে গেল, দেখতে দেখতে চল্লিশ হবে, তারপর চল্লিশের ওপারে হেলে পড়বে। আফটার ফরটি মানেই দাঁত আলগা হওয়া, চুল উঠে যাওয়া, চোখে দোতলা চশমা পরা, ব্লাড সুগার আর প্রেশারের জন্যে উৎকণ্ঠা, মানে ‘শেষের সে-দিনের জন্যে’ ঘন ঘন তাকানো।
অসুখের পর প্রেমকিশোর মনে মনে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। বন্ধুদের স্ত্রীর খোঁজ-খবর নেওয়া, সেবাযত্ন করা, পাশে বসে গল্প করা, এই সব দেখে শুনে তার মনে হল, বিয়ের একটা প্রয়োজন আছে। হাজার হোক, বউ থাকা মানে একজন কেউ থাকা, সে অন্তত প্রেমকিশোরকে দেখাশোনা করতে পারবে, অসুখ-বিসুখে মাথার কাছে বসে থাকবে, আর প্রেমকিশোর মারা যাবার পর অন্তত এই বাড়িটার মালিক হবে।
প্রেমকিশোর বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। বন্ধুদের বলল, বেশ, বিয়ে আমি করব। কিন্তু মেয়ে নয়—মহিলা। বয়েস মিনিমাম পঁয়ত্রিশ হতে হবে। মোটামুটি দেখতে হলেও চলে যাবে, তবে মোটা চলবে না। জাতের ব্যাপারে আমার কোন প্রেজুডিস নেই। মহিলাকে শিক্ষিতা হতে হবে। আর আমার অন্য শর্ত, বাপের বাড়ির গুষ্টি আমি অ্যালাও করব না।
বন্ধুরা বলল, ঠিক আছে; একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দি—দেখা যাক।
তিন মাসে তিন রবিবার বাংলা কাগজে প্রেমকিশোরের বিয়ের পাত্রী চাই বিজ্ঞাপন বেরুল। চিঠি এল শ’ দেড়েক। বন্ধুরা সর্ট করল, চিঠি পড়ল, আলোচনা করল, কোন মেয়েকেই পছন্দ হল না প্রেমকিশোরের।
দেখতে দেখতে আরও মাস দুই কাটল। এমন সময় আচমকা প্রেমকিশোরই ইংরেজি কাগজ থেকে এক বিজ্ঞাপন এনে হাজির করল। এমন বিজ্ঞাপন সচরাচর চোখে পড়ে না, আদপেই পড়ে কি না কে জানে, মেয়েপক্ষ নিজেই নিজের বিজ্ঞাপন দিয়েছে।
ব্যাপারটা প্রেমকিশোরকে খুবই রোমাঞ্চিত করেছিল। এই তো হওয়া উচিত। কোন ন্যাকামি নেই, একেবারে সোজাসুজি ব্যাপার। মেয়ে লিখেছে: ‘আমার বয়েস ছত্রিশ, ডক্টরেট করার পর আমি আরও রিসার্চ করছি, আমার গায়ের রং এবং চেহারা সাধারণ। যে কোন ভদ্রলোক, বয়েসে অন্তত আমার সমবয়স্ক হবেন, এক আধ বছরের ছোটতেও আপত্তি নেই। অবশ্যই তিনি শিক্ষিত ও উপার্জনসক্ষম হবেন, বিবাহের ব্যাপারে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। পছন্দ হলে ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে আলাপ-পরিচয় করব।’
বন্ধুরা বিজ্ঞাপন দেখে রীতিমত ভড়কে গিয়েছিল। বলেছিল, এ তো মাইরি ডেঞ্জারাস মহিলা।
প্রেমকিশোর বলেছিল, এমন মেয়েই আমি সারা জীবন ধরে খুঁজছি। স্ট্রেট, ডিরেক্ট, প্রোগ্রেসিভ।…তোদের ন্যাকামি নেই, লজ্জা নেই, বাজে টলানি নেই। একেই শালা মডার্ন ক্যারেকটার বলে। রিয়েল লিব মুভমেন্ট।
বন্ধুরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে বলল, তা হলে লেগে পড়।
প্রেমকিশোর লেগে পড়ল। চিঠি লিখল পোস্ট বক্স-এর নম্বরে। দিন কুড়ি বাইশ পরে জবাব পেল। নাচতে নাচতে বন্ধুদের এসে বলল, ইন্টারভিউতে ডেকেছে রে। পার্ক স্ট্রিটে চিনে দোকানে ইন্টারভিউ হবে।
গুহ বলল, “জেনারেল নলেজের বইটা পড়ে যাস।”
প্রেমকিশোর বলল, “হ্যাত, আমি তার চেয়েও একটা টেরিফিক বই পড়ছি, আমেরিকান বই। কী নাম জানিস? হাউ টু উইন এ উইমেন ইন বেড অ্যান্ড আউট অফ বেড?”
গুহ বলল, “বেডটাও কি সাজিয়ে ফেলেছিস?”
প্রেমকিশোর বলল, “ডোন্ট বি ভালগার। সি ইজ এ লেডি…মাইন্ড দ্যাট।”
এরপর মাস দেড়েকের মধ্যে প্রেমকিশোর রেজেস্ট্রি করে বিয়ে করে ফেলল। বন্ধু আর বন্ধুর স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের ভূরিভোজ দিল। বাড়িতেই। তার স্ত্রীকে দেখলেই সমীহ করতে ইচ্ছে করে। মোটামুটি লম্বা চেহারা, ছিপছিপে গড়ন, চোখে মোটা চশমা, ভীষণ সিরিয়াস মুখ, ধারালো চোখ, নাকটা লম্বা, মাথার চুল বব করা। কথার মধ্যে দু-চারটে হিন্দি চলে আসে। শাড়ির চেয়ে ঢিলে প্যান্ট আর মেয়ে-শার্ট পরতে পছন্দ করে বেশি। নাম, শশিকলা।
শশিকলা নামটা বন্ধুদের পছন্দ হয়নি। এ আবার কি নাম? পুরানো।
প্রেমকিশোর বলল, “শুধু শশী বলবি। কী সুন্দর। ও আবার হিন্দি দেশেই মানুষ কি না—ওই রকমই নাম—ওরা বলে শাশি…”
মন্মথ বলল, “ভালই হয়েছে। প্রেম-শশী। তোরা মিলে যা ভাই, আমরা চক্ষু সার্থক করি।”
সেই ঘটনার পর আজকের এই ঘটনা। প্রেমকিশোর বিয়ের দশ বারো দিনের মাথায় রক্ত-আমাশায় ভোগা রোগীর মতন চিঁ চিঁ করতে করতে ছুটে এসেছে বন্ধুদের কাছে। এই কদিন যে বন্ধুরা খোঁজখবর নেয়নি, তার কারণ, প্রেমকিশোর বলে রেখেছিল সে নতুন বউ নিয়ে হনিমুন করতে পুরী ওয়ালটেয়ার যাবে। বন্ধুরা ভেবেছিল, প্রেমকিশোর কলকাতায় নেই, প্রেম-মিলন করে বেড়াচ্ছে সমুদ্রের ধারে ধারে।
দুই
বাড়ির ভেতর থেকে চা এসে গিয়েছিল।
চা আর সিগারেট খেতে খেতে সুবীর বলল, “এবার ব্যাপারটা বল?”
প্রেমকিশোর আস্তে আস্তে চা খাচ্ছিল। সিগারেট ধরিয়ে নিল একটা। তারপর বলল, “সব কথা বলতে হলে মহাভারত হয়ে যাবে। অত কথা বলতে পারব না, সময় নেই। ঘণ্টা দুয়েকের ছুটি নিয়ে পালিয়ে এসেছি।”
‘ছুটি নিয়ে পালিয়ে এসেছি মানে?” মন্মথ জিজ্ঞেস করল।
“আর বলিস না ভাই, আমি এখন হিউম্যান গিনিপিগ। চব্বিশ ঘণ্টা ওই মেয়েছেলের অবজারভেশানে আছি। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। একেবারে চোখে চোখে রেখেছে।”
বন্ধুরা হাঁ হয়ে গেল। পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। এ রকম হবার কথা নয়। তবে কি শশিকলা তার ছত্রিশ বছরের জমানো প্রেম দিয়ে প্রেমকিশোরকে জমিয়ে ফেলতে চাইছে? এ তো ভাবাই যায় না আজকালকার দিনে। এক মুহূর্তও চোখের আড়াল হতে দেবে না, হলেই অচেতন হবে—এসব বৈষ্ণব কাব্যে হত! দারুণ ব্যাপার তো!
সুবীর বলল, “তুই বলছিস কি, প্রেম? এ তো তোর ভাগ্য! ছত্রিশ বছর বয়েসের মহিলা, তুই তার ফার্স্ট হাজবেন্ড অ্যান্ড লাভার! ভেবে দেখ, যৌবন যায়-যায় বলে কেমন সলিড প্রেমে তোকে ধরে রাখতে চাইছে শশী।’’
প্রেমকিশোর ক্ষুন্ন হয়ে বলল, “যথেষ্ট হয়েছে ভাই, কাটা ঘায়ে আর নুনের ছিটে কেন?”
মন্মথ হাত তুলে বন্ধুদের বলল, “দাঁড়া, তোরা চুপ কর। আমি ব্যাপারটাকে বুঝি।’’বলে সে প্রেমকিশোরের দিকে তাকাল, বলল, “শশী তোকে চব্বিশ ঘণ্টা চোখে চোখে রাখছে এইটেই তোর মেইন কমপ্লেন?”
“হ্যাঁ, আমার আরও হাজারটা কমপ্লেন আছে।’’
“একটা একটা করে বল। নয়ত গুলিয়ে ফেলব।…তোর অফিস কবে?”
“এক মাস ছুটি নিয়েছিলাম। মাত্র পনেরো দিন হয়েছে। আরও পনেরো দিন-মর্নিং টু নাইট ওর কাছে থাকতে হবে। বাবা গো, আমি মরে যাব।”
গুহ বলল, “গোড়া থেকে শোনাই ভাল, মন্মথ। আমার মনে হচ্ছে, প্রেম নিজের মতন করে বলুক। তার যেখান থেকে ইচ্ছে।”
সুবীর বলল, “সেই ভাল। …প্রেম, তুই প্রথম থেকে—তোর যা বলতে ইচ্ছে করে। বল। আমরা শুনছি।”
প্রেমকিশোর চা শেষ করল। একটা সিগারেট শেষ করে আরও একটা ধরিয়ে নিল। তারপর করুণ মুখ করে বলল, “ভাই, প্রথম দিন, দি ভেরি ফার্স্ট নাইট আমরা তো তোদের মতন ফুলশয্যা করিনি। তবু কিছু ফুল-টুল ছিল, নতুন চাদর, নতুন বালিশ, সেন্ট-টেন্ট একটু ছড়িয়ে দিয়েছিলাম বিছানায়। তোরা সব খাওয়া-দাওয়া শেষ করে চলে এলি, আমরা সাড়ে এগারোটা নাগাদ বিছানায় এলাম। আমার বুকের মধ্যে একটা টেনিস বল যেন লাফাচ্ছিল ভাই। রিয়েলি, কেমন যেন আবেশও লাগছিল, আবার নার্ভসও লাগছিল। সেই যে বইটা পড়েছিলাম, হাউ টু উইন এ উইমেন ;সেই টেকনিকে প্রথমেই খুব স্মার্ট ভাবে শশীকে বললাম, তোমার জন্যে দুটো জিনিস কিনে রেখেছি—বলে দামি পোখরাজ বসানো একটা আংটি, আর সাদা পাথর বসানো কানের গয়না ওর হাতে তুলে দিলাম। আংটিটা পরিয়ে দিলাম। কানের গয়নাটা শশী রেখে দিল। শুরুটা ভালই হল। দুজনে বিছানায় বসলাম। দু-পাঁচটা কথা হল। আমি বেশ হেসে হেসে কথা বলছিলাম। হঠাৎ ভাই শশী আমায় কি বলল জানিস?”
“কী?’’
“বলল, মানে আমায় জিজ্ঞেস করল, তোমার অত চোখ পিটপিট করে কেন? মিনিটে তিরিশ বার?”
সুবীর বলল, “সে কি রে?”
প্রেমকিশোর বলল, “হ্যাঁ ভাই, ফর গডস সেক, ওই কথা বলল। বলার পর আমার চোখ পিটপিট বেড়ে গেল; মিনিটে থার্টি থেকে বাড়তে বাড়তে ফর্টি ফিফটি হয়ে গেল।”
“তারপর?”
“তারপর আরও একটা ব্লো মারল।”
“ব্লো? মানে ঘুঁষি।”
“ঘুঁষি নয়, দাবড়ানি। বলল, কথা বলার সময় তোমার খানিকটা তোতলামি আছে, তুমি প্রপার ওআর্ড মনে করতে পারো না, ইউ মিস ইট। হোয়াই?”
মন্মথ বলল, “যাঃ বাব্বা। ফুলশয্যা করতে বসে এই ডায়লগ?”
প্রেমকিশোর পরম দুঃখীর মতন বলল, “হ্যাঁ, ভাই, এই ডায়লগ। রাত দেড়টা পর্যন্ত আমার ডিফেক্ট সম্পর্কে কত রকম কি শুনতে হল। তারপর বাতি নিভিয়ে শুলাম।”
গুহ এবার একটু গলা ঝাড়ল।
প্রেমকিশোর মাথা নেড়ে বলল, “গলা ঝাড়ার দরকার নেই। যা ভাবছ তা নয়। আমি তখন এত নার্ভাস হয়ে গিয়েছি একটার পর একটা অ্যাটাকে যে আমার কোলাপ্স করার অবস্থা। একেবারে শালা ডেড হয়ে শুয়ে থাকলাম। আর শশী একেবারে চাঁদের মতন ঢলে পড়ল। ও দিব্যি ঘুমিয়ে পড়ল। আমি সারারাত জেগে থাকলুম।”
গুহ বলল, “টাচ লাইনের বাইরে বেরুতে পারলি না?”
“টাচই হল না তো বাইরে!”
কেসটা যে রীতিমত গোলমেলে সুবীর হাজরা যেন তা বুঝতে পারল। বুঝে চুপ করে থাকল।
প্রেমকিশোর তার মাথার রুক্ষ চুলে আঙুল চালাল। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলল। বুকে হাত বোলাল।
মন্মথ বলল, “পরের দিন কী হল?”
“পরের দিন সকাল থেকেই আমার ওপর অবজারভেশান শুরু হয়েছে।’’
“মানে?”
“মানে আমার হাঁটা, চলা, কথা বলা, দাঁত মাজা, খাওয়া, শোওয়া, জামাকাপড় পরা, তাকানো সব এখন শশিকলার অবজারভেশানে রয়েছে।”
“কেন?”
“শশী সাইকোলজি নিয়ে ডক্টরেট করেছে।”
“কোন ইউনিভার্সিটি?”
“বিদর্ভ গন্ধর্ব কোন একটা জায়গা থেকে হবে। বছর কয়েক ওদিকেই কোথাও সাইকো-অ্যাট্রিস্ট হিসেবে কাজ করেছে। তারপর কলকাতায় এসেছে। এখন ওর হায়ার রিসার্চ চলছে।”
“হায়ার রিসার্চ?”
“তাই তো বলে ভাই, বিয়ের পর পাঁচ বাক্স বই, দু বাক্স কাগজপত্র, এক বাক্স নানা ধরনের খেলনা টাইপের জিনিস আর সব কি কি এনেছে।”
“এখন কী তোকে নিয়ে রিসার্চ করছে?”
“হ্যাঁ ভাই। আমি এখন শশিকলার হিউম্যান গিনিপিগ। চব্বিশ ঘণ্টা পিছনে লেগে আছে।”
সুবীর কপালে করাঘাত করে বলল, “সর্বনাশ!”
প্রেমকিশোর বলল, “শুধু সর্বনাশ নয়, আমার জীবননাশ হতে বসেছে।”
গুহ মাথা চুলকে বলল, “তোকে নিয়ে কী রিসার্চ করছে, প্রেম? রিসার্চের সাবজেক্টটা কী?”
প্রেমকিশোর বলল, “ভাই, আমি সাইকোলজির কিছু বুঝি না। তবে কথাবার্তা শুনে যা মনে হয় মানুষের ডেন্টাল ফরমেশান তার হিউম্যান নেচারকে ইনফ্লুয়েন্স করছে—সেই নিয়ে এক গবেষণা।”
কথাটা শোনামাত্র তিন বন্ধু এক সঙ্গে আঁতকে উঠল। আঁতকে উঠে তিনজনেই তাদের দাঁত উন্মুক্ত করে বসে থাকল।
প্রেমকিশোর বলল, “ব্যাপারটা আমিও বুঝি না। তবে শশীর কথা থেকে মনে হয়, মানুষের দাঁতটাই আসল; দাঁত দেখে তার স্বভাব প্রকৃতি—ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল, দুইই বলে দেওয়া যায়।”
সুবীর বলল, “বলিস কী! দাঁত দেখে শুনেছি ঘোড়ার বয়েস আন্দাজ করা যায়। আমরা কী ঘোড়া?”
প্রেমকিশোর সদুঃখে বলল, “ঘোড়াও ভাল; আমরা ঘোড়ারও অধম; গাধা।”
গুহ আর মন্মথ দাঁতে দাঁত বাজাল। দেখল, দাঁতগুলো শক্ত না নরম।
মন্মথ বলল, “তোকে কী করতে হয়? বউয়ের কাছে দাঁত বের করে বসে থাকতে হয়
মাথা হেলিয়ে প্রেমকিশোর বলল, “একজ্যাক্টলি। সকালে ঘণ্টা দেড়েক; দুপুরে ঘণ্টাখানেক। আর রাত্রে কম করেও দু’ ঘণ্টা।”
সুবীর উৎকট এক শব্দ করল। মনে হল, যেন বাব্বা বলল। তারপর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, “কীভাবে থাকিস একটু দেখা তো।”
প্রেমকিশোর বলল, “কী ভাবে আর থাকব! শশী চেয়ার টেবিল নিয়ে বসে থাকে, টেবিলে দিস্তে দিস্তে কাগজ, হাতে কলম। আমি হাত তিনেক দূরে একটা টুলের ওপর দাঁত বের করে বসে থাকি। কখনো তার দিকে তাকাই, অবশ্য তাকাতে বললে, আর না হয় জানলার দিকে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে।…শশী দেখে আর কাগজে কি লেখে। দেখে আবার লেখে। মাঝে মাঝে এসে ফরসেপ দিয়ে মাড়ি উঠিয়ে ভেতর দিকের দাঁত দেখে যায়।”
বন্ধুরা থ মেরে গেল। এমন ঘটনা তারা জীবনে শোনেনি। মাথায় কিছু আসছিল না।প্রেমকিশোরের দুঃখে তারাও বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলতে লাগল।
প্রেমকিশোর বলল, “এখন বল, আমি কী করি! আমার ত্রিশূল পর্বতে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই।…সাধে কি ব্যাচেলার ছিলাম।”
কথাটা ঠিকই। প্রেমকিশোর যতদিন অবিবাহিত ছিল, বেশ ছিল, বিয়ে করেই ডুবল। শুধু ডুবল নয়। পনেরো দিনেই যে হাল তাতে এই অবস্থা চলতে থাকলে মাসখানেকের মধ্যেই ওকে নিমতলায় গিয়ে দাঁড়াতে হবে।
তিন বন্ধুই গুম। মেজাজটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। প্রেমকিশোরের এই বিপদে কি করবে, বুঝে উঠতে পারছে না।
শেষে মন্মথ প্রেমকিশোরের ওপরই চটে গেল। বলল, “তখনই তোকে বলেছিলাম, এইসব বিয়ে করিস না। মেয়েছেলে নিজের বিয়ের বিজ্ঞাপন নিজে দিচ্ছে, ব্যাপারটা গোলমেলে। তুই বেটা এমন উজবুক, আমাদের কথা শুনলি না, দারুণ দারুণ বলে নাচতে লাগলি। এখন বোঝ, সামলা তোর শশিকলাকে। দন্ত শোভা প্রদর্শন করে বসে থাক।” রাগের মাথায় মন্মথ ভাল ভাল বাংলা বলে ফেলল। এক কালে কাব্যচর্চা করতে বলেই বোধহয়।
প্রেমকিশোর অপরাধীর মতন বলল, “ভাই, যা করেছি ভুল করেছি। গাধার মতন কাজ করেছি। আর করব না। কিন্তু এখন আমার কী হবে? হয় ত্রিশূল, না হয় সুইসাইড। সুইসাইড করতে আমার ইচ্ছে নেই। বড় পেইনফুল। মারা যাবার পরও কাটাকাটি করবে। শরীরটাকে আমি মুদ্দাফরাসের হাতে দিতে চাই না।”
সুবীর বলল, “শোন, তোর প্রবলেমটা ভেরি ডিফিকাল্ট। ঝট করে ভেবে কিছু বলা যাবে না। লেট আস থিংক ওভার দি ম্যাটার। আমরা ভাবি। আলোচনা করি। পরে তোকে একটা কিছু বলব। কী বল, গুহ?”
গুহ বলল, “হ্যাঁ, ব্যাপারটা কঠিন। ভাবতে হবে।”
“তোরা আমায় ধাপ্পা দিচ্ছিস?” প্রেমকিশোর সন্দেহ প্রকাশ করল।
“না, না, ধাপ্পা দেব কেন! তুই আমাদের পুরনো বন্ধু। তোর লাইফ মিজারেবল করে একটা মেয়ে পার পেয়ে যাবে—তা হয় না। এটা চ্যালেঞ্জ। আমরা পুরুষ হয়ে একটা মেয়ের বাঁদরামির কাছে হেরে যাব?”
“বাঁদরামি বলিস না ভাই”, প্রেমকিশোর বাধা দিয়ে বলল, “হাজার হোক লিগাল ওয়াইফ।’’
“যা যা বাজে বকিস না; ওয়াইফের নিকুচি করেছে। তুই শনিবার আয়।” “কেমন করে আসব?”
“ধাপ্পা মেরে আসবি শালা। আমরা থাকব। তখন তোকে বলব কী করা যায়। বুঝলি ?…আর দেরি করিস না, পালা। তোর শশিকলা নাইট সিটিংয়ের জন্যে বসে আছে।”
প্রেমকিশোর উঠে পড়ল। দু’ ঘণ্টার মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। ঘড়ি দেখল। তারপর বলির পাঁঠার মতন কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে গেল। যাবার সময় বলে গেল, “ভাই, তোরাই আমার শেষ ভরসা। যা হয় করিস। হয় বাঁচাস, না হয় মেরে ফেলিস। আচ্ছা যাই।”
প্রেমকিশোর চলে যাবার পর তিন বন্ধু পরস্পরের দিকে তাকাল। তিনজন তিনজনকে দাঁত দেখাল। তারপর গালে হাত দিয়ে বসে থাকল।
তিন
প্রেমকিশোর যা বলেছিল সেটা যে মিথ্যে নয়, পরের দিনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে সেটা বোঝা যাবে।
পরের দিন সকালে প্রেমকিশোর ঘুম থেকে উঠে বাথরুমে গেল। ফিরে এসে চা খেতে বসল বারান্দায়।
টেবিলে চা সাজিয়ে শশিকলা বসে ছিল। বারান্দায় যথেষ্ট আলো রয়েছে; রোদও এসেছে। ছোট টেবিল। আলো আর রোদ যেদিকে বেশি প্রেমকিশোরের বসার চেয়ার সেদিকেই। উল্টো দিকে শশিকলা বসে আছে। তার একপাশে টেবিলের ওপর কিছু সাদা কাগজ ক্লিপ দিয়ে আঁটা। পাশে একটা ফাউন্টেন পেন। টেবিলে চায়ের পট, দুধ, চিনি ; আর তিন চার রকম খাবার। একেবারে কড়কড়ে টোস্ট ; এক প্লেট শক্ত মটর, গোটা চারেক কলা। সকালে কি কি খাবে প্রেমকিশোর শশিকলা ঠিক করে রাখে আগে থেকেই।
প্রেমকিশোর চেয়ারে বসে গোবেচারার মতন মুখ করে হাসল একটু। তারপর দু’ পাটি দাঁত বের করে বসে থাকল।
শশিকলা ডাক্তারের মতন তীক্ষ্ণ চোখ করে দাঁত দেখল। তারপর বলল, “ক’ দাফে করেছ? টু অর থ্রি?”
প্রেমকিশোর আঙুল তুলে দুই দেখাল।
“আই টোল্ড ইউ টু মেক থ্রি। মনে থাকে না?”
প্রেমকিশোর বলল, “নতুন পেস্ট; মাড়ি জ্বলে যাচ্ছিল।”
“জ্বলে যাচ্ছিল! বাচ্চে কি মাফিক বাত মাত্ বোলো জি।”
শশিকলা কলম তুলে নিয়ে কাগজে কি যেন লিখল। শশিকলার মুখের চেয়ে চশমা যেন বড়, মোটা মোটা কাচ, চৌকোনো ফ্রেম, কাচের মধ্যে আবার গোল গোছের অস্পষ্ট দাগ। নাক প্রচণ্ড লম্বা। বব করা চুল। পাঁশুটে রং চুলের। গায়ে হালকা নীল শাড়ি, আঁটসাঁট করে পরা, গায়ের ব্লাউজ ধবধবে সাদা। চোখে-মুখে অবাঙালিয়ানার ছাপ আছে। মুখ দেখতে মন্দ নয়, কিন্তু সারা মুখে কেমন রুক্ষতা রয়েছে। চোখ দুটো ভীষণ তীব্র লাগে।
শশিকলা চা ঢালবার আগে হাত দিয়ে কলার প্লেটটা দেখাল। বলল, “কেলা খাও পহেলে।’’
প্রেমকিশোর বলল, “তুমি আমার কাছে হিন্দি বোলো না। আমি বুঝতে পারি না। আইদার ইউ ম্পিক ইন ইংলিশ অর ইন বেঙ্গলি।’’
শশিকলা স্বামীর দিকে তাকাল। “অল রাইট। কোলা খাও।”
প্রেমকিশোর চটে গেল। বাংলা নিয়ে ঠাট্টা। তুমি কোন মহারানি গো যোধপুরের? কলার প্লেট টেনে নিয়ে বলল, “কোলা নয় কলা। শশিকোলা কিংবা শশিকেলা বললে তোমার শুনতে ভাল লাগবে?”
শশিকলা চোখের চাউনিতে যেন বিস্ময় ফোটাল। বলল, “আচ্ছা! ইউ আর শোয়িং সাম ক্যারেজ।”
প্রেমকিশোর কলার খোসা ছাড়িয়ে মুখে দিল।
শশিকলা চা ঢালতে লাগল। হঠাৎ শশিকলা বলল, “স্টপ।”
প্রেমকিশোর ঠোঁট বন্ধ করল, মুখের মধ্যে কলা।
শশিকলা বলল, “দাঁত দেখাও।”
প্রেমকিশোর দাঁত বের করল। মুখের কলা গলায় আটকে যায় আর কি!
শশিকলা দেখল। তারপর আবার কলম তুলে কি লিখল। লেখা শেষ হয়ে গেল। “ফ্রম সফট টু হার্ড। আজ তুমি প্রেম, নার্ম চিজ খাবে ফাস্ট, উসকি বাদ হার্ড, হার্ডর। আমি তোমায় অবজার্ভ করব। সমজ মে আয়া?”
প্রেমকিশোর মাথা নাড়ল। —না।
“কাহে?”
“হিন্দি আমি বুঝি না। বাংলায় বললা।”
শশিকলা দু মুহূর্ত যেন কি ভাবল, তারপর বলল, “সরি।” বলে বাংলায় বলল “পহেলে কলা খাবে নার্ম চিজ; নেক্সট খাবে টোস্ট, বাদ মে মটর।”
কাল বন্ধুদের কাছ থেকে ঘুরে আসার পর প্রেমকিশোরের মনে খানিকটা সাহস এসেছিল। তা ছাড়া কাল রাত্রে সে স্বপ্ন দেখেছে, প্রেমকিশোর ঝোলাঝুলি কাঁধে করে লাঠি হাতে গেরুয়াশোভিত মুণ্ডিতমস্তক হয়ে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে হিমালয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে। খুব সম্ভব ত্রিশূল পর্বতেই ডেরা বাঁধতে যাচ্ছে। স্বপ্নটা তাকে তাড়া দিচ্ছিল, চাগিয়ে দিচ্ছিল। সংসার যদি ছাড়তেই হয় সে বীরের মতন ছাড়বে, ভীরুর মতন নয়। ভেতরের এই বিদ্রোহ প্রেমকিশোরকে সামান্য সাহসী করে তুলছিল।
কলা খেয়ে আরও কলার খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে প্রেমকিশোর বলল, “তোমার মুখে বাংলা শুনতে আমার খুব ভাল লাগে, শশী। প্লিজ বাংলাতেই কথা বলো।”
শশিকলা প্রেমকিশোরের দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিল।
মাখন লাগানো বিস্কিট নিল শশিকলা, মুখে দিল, দিয়ে দাঁতের ডগায় ভাঙল। চমৎকার দাঁত শশিকলার, ঝকঝকে, সুবিন্যস্ত, সাজানো। শশিকলা ধীরে ধীরে খায়, ঠোঁট সামান্য ফাঁক করে।
প্রেমকিশোর সাহস করে বলল, “তুমি আমায় একটু বুঝিয়ে দেবে।”
“কী?”
“এই দাঁতের সাইকোলজিটা?” বলে প্রেমকিশোর স্ত্রীকে সর্বোৎকৃষ্ট তেল দিচ্ছে এ রকম একটা ভাব করে বলল, “তুমি দারুণ লার্নেড, অর্ডিনারি মেয়েদের মতন নও, তোমার সাংঘাতিক অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার, রিসার্চের সাবজেক্টটাও ভেরি ডিফিকাল্ট। আমার দারুণ ইন্টারেস্ট লাগছে।”
শশিকলা কথাটা কানে তুলল না। বলল, “নার্ম জিনিস যখন খাও তখন তোমার দাঁতের ফিলিং কেমন হয়?”
প্রেমকিশোর চুপ। জিভটা দাঁতের ওপর বুলিয়ে নিল। তারপর বলল, “নরম জিনিস মানে ডাল ভাত পেঁপে কলার কথা বলছ?”
“জরুর।”
“নাথিং স্পেশ্যাল। কিছুই ফিল করি না। আরও নরম কিছু খেতে পারলে ডিফারেন্সটা বুঝতে পারতাম।”
“আরও নার্ম?”
প্রেমকিশোরের ইচ্ছে হল রহস্যময় দৃষ্টিতে একবার শশিকলার দিকে তাকিয়ে চোখ টেপে। সাহস হল না। সাহসের বাড়াবাড়ি ভাল নয়। প্রেমকিশোর বলল, “আরও নরম কিছু থাকতে পারে।”
“এনি ফুট?”
“ফল!…হ্যাঁ তা ফলও বলা যায়।”
“তো বোলো— ’’
মাথা চুলকে প্রেমকিশোর বলল, “বিম্বোধর!”
“কেয়া?”
“দ্যাটস এ ফুট। ক্ল্যাসিকাল ফুট। ওরই বড়সড় ফল হল পয়োধর।”
“আমার মালুম নেই!”
“যেমন ধর খরমুজ আর তরমুজ। দে আর মোর অর লেস এ সেম কাইন্ড অফ ফ্রুট। বাট দে ডিফার ইন সাইজ অ্যান্ড টেস্ট।”
“তুমি কী নাম বললে জি?”
“বিম্বোধর আর পরোধর।”
“আই হ্যাভ নেভার হার্ড অফ ইট? কলকাত্তায় পাওয়া যায়?”
প্রেমকিশোরের ভীষণ হাসি পাচ্ছিল। হাসি চাপতে না পেরে সে পটাস করে একবার চোখ টিপে দিল। মনে মনে বলল, শশী, কলকাতায় কেন এই বাড়িতেই পাওয়া যায়। তুমি মাইরি কী ক্রুয়েল।
শশিকলা ঝপ করে কলম তুলে নিল! বলল, “নার্ম ফুড খাবার পর তোমার আঁখ নাচে। দ্যাটস ভেরি ফানি। আই মাস্ট মেক এ নোট অফ দিস পারটিকুলার এফেক্ট…” বললে বলতে শশিকলা খসখস করে নোট লিখতে লাগল।
প্রেমকিশোর বিপদ বুঝে আবার চোখ পিটপিট শুরু করল।
টোস্টে হাত দিল প্রেমকিশোর। কড়কড়ে টোস্ট। মাখন দেওয়া হয়নি। মাখনে নরম হয়ে যেতে পারে বলেই বোধহয়।
প্রেমকিশোরের দাঁত অত মজবুত নয়। রীতিমত কষ্ট করে খেতে হচ্ছিল। এরপর শক্ত মটরদানা খেতে হবে। চোখে জল চলে আসছিল প্রেমকিশোরের। শশিকলা প্রথম কাপ চা শেষ করে আরও এক কাপ চা ঢেলে নিল। নিয়ে হাফ—বয়েল ডিমের প্লেটটা টেনে নিল।
প্রেমকিশোর মনে মনে গালাগাল দিয়ে বলল, শালা, আমার বেলায় সব শক্ত, আর তোমার বেলায় নরম! ঠিক আছে, দু’ দিন সুখ করে নাও, তারপর দেখবে প্রেম কোথায় যায়, সোজা ত্রিশূল পর্বতে চলে যাবে।
হাফ—বয়েল খেতে খেতে শশিকলা বলল, “তুমি আমার থিয়োরির কুছ জানতে চাইছিলে?” প্রেমকিশোর মাথা নাড়ল। তার দাঁত ব্যথা করছে। টোস্ট এত কড়কড়ে হয়? এ একেবারে লোহা!
শশিকলা তার দাঁতের থিয়োরি বোঝাতে লাগল। মানুষের দাঁতই তার চরিত্র, দাঁতই তার ইমোশানকে বুঝিয়ে দেয়। যেমন, যাকে আমরা সুন্দর বলি—ছেলেই হোক আর মেয়েই হোক—সাধারণত তাদের দাঁত সুন্দর, ঝকঝকে, সুবিন্যস্ত। যাদের আমরা দেখতে খারাপ বলি তাদের দাঁত বেশির ভাগ সময়েই বিশ্রী। যথার্থ সুন্দরী কোন মেয়ের দাঁত খারাপ হতে পারে না, যেমন হেলেনের দাঁত ছিল সোনার মতন ঝকঝকে, ক্লিয়োপেট্রার দাঁত ছিল মুক্তোর মতন, কিন্তু দাঁতের ডগা ছিল ধারালো ; যিশুর ছবিতে তাঁর দাঁতের যে আকার তাতে বোঝা যায় এমন মহাপুরুষ বিরল। শ্রীরামকৃষ্ণের হাসির সময় তাঁর যে ক’টি দাঁত ছবিতে দেখা যায়—তাতে বোঝা যায়, এমন আত্মভোলা সরল সাধক মানুষ আর দ্বিতীয়টি হয় না।
শশিকলা দাঁতের সাইকোলজি বোঝাতে বোঝাতে বলল, “আদমি শয়তান হলে দাঁত বড়া হয়, এজ শারপ হয়, ফরমেশান খারাপ হয়। ইসলোক ক্রিমিন্যাল। বাচ্চারা ইনোসেন্ট, তারা হাসলে দাঁত দেখো, সো বিউটিফুল। ইউ নো প্রেম, অল দি হিউম্যান ইমোশান্স অফ পেইন অ্যান্ড প্লেজার—দাঁতকে রিঅ্যাক্ট করায়। আগর তুমি গোসা করো—দাঁতে দাঁত ঘষবে, তুমি মজা পাও, তুমি হাসো, অ্যান্ড সো অন…হাজারো একজাম্পল আছে জি।”
প্রেমকিশোর মটরদানা চিবোচ্ছিল; একটা শক্ত মটর খটাস করে দাঁতে লাগল। দাঁতের একটা পাশ ভেঙে গেল। ব্যথায় লাফিয়ে উঠল প্রেমকিশোর।
শশিকলা বলল, “কেয়া হুয়া?”
প্রেমকিশোর বলল, “মর গিয়া।”
চার
শনিবার দিন প্রেমকিশোর যথাসময়ে বন্ধুদের কাছে হাজির হল। তার ডানদিকের গাল সামান্য ফোলা, রুমাল চাপা দিয়ে রেখেছিল।
বন্ধুরা প্রেমকিশোরের জন্যেই অপেক্ষা করছিল; সে আসতেই সুবীর অভ্যর্থনা করে বলল, “আয় আয়, তোর জন্যেই ভাবছিলাম।”
প্রেমকিশোর গালের পাশ থেকে রুমাল সরাল।
মন্মথ বলল, “কী হয়েছে রে? ফোলা ফোলা দেখছি!”
প্রেমকিশোর বলল, “তোদের কাজ দেখে যাবার, তোরা শুধু দেখে যা; আর আমি তোদের চোখের সামনে তিলে তিলে মরি।”
গুহ বলল, “হয়েছে কী বলবি তো?”
দীর্ঘশ্বাস ফেলে প্রেমকিশোর গাল ফোলার বিবরণ দিল। বলল যে, শশিকলার হুকুমে সে শক্ত মটরদানা চিবিয়ে খাচ্ছিল। শক্ত জিনিস খাবার সময় তার দাঁত কেমন ব্যবহার করছে শশিকলা সেটা দেখছিল। হঠাৎ একটা মটরদানা এমন বেকায়দায় কষদাঁতের একটাতে লেগে যায় যে, নীচের দাঁতের একটা চাকলা ওপর থেকে উঠে বেরিয়ে গেল। মনে হল, ব্রহ্মতালু পর্যন্ত নড়ে গেল।
প্রেমকিশোর বলল, “সে কী যন্ত্রণা ভাই, ছুরির মতন ধারালো একটা পাশ গালে লেগে ঘা হয়ে গেল দুপুরের মধ্যেই। বিকেলে ডেন্টিস্টের কাছে গিয়ে ঘষিয়ে এলাম। ভাঙা জায়গাটায় এনামেল নেই, কিছু লাগলেই কনকন করছে, জল পর্যন্ত খেতে কষ্ট হয়। ওষুধ চালাচ্ছি। ফোলা আগের চেয়ে অনেকটা কমেছে।”
সুবীর বলল, “তোর বউকে এখনও দাঁত দেখাচ্ছিস?
“মাঝে মাঝে দেখাতে হয়, সিটিং বন্ধ আছে। এখন নরম নরম জিনিস খাইয়ে মাঝে মাঝে দেখছে।’’
“কী খাওয়াচ্ছে?”
“ঢেঁড়স সেদ্ধ, পেঁপে সেদ্ধ, কলা সেদ্ধ,…এইসব।”
“তোর দাঁত ঠিক হয়ে গেলে আবার ধরবে?”
“ধরবে মানে, গলা টিপে ধরবে। এই দু-তিন দিন ঠিক মতন সিটিং হচ্ছে না বলে বেশ রেগে আছে।’’
গুহ চায়ের জন্যে হাঁক ছাড়ল।
মন্মথ বলল, “তুই কিছুই করতে পারছিস না, প্রেম?”
“নাথিং।” মাথা নাড়ল প্রেমকিশোর বিরস মুখে, “তোদের এখান থেকে ফিরে গিয়ে পরের দিন একটু গরম নিচ্ছিলাম, শালা দাঁত ভেঙে গেল।’’
সুবীর মাথা নেড়ে বলল, “ব্যাপারটা আমি বুঝতেই পারছি না। বউকে বললাম, হ্যাঁ গো, তুমি তো আমার মুখ দেখেই জীবন কাটাবে বলেছিলে, কিন্তু প্রেমের বউ বলেছে, সে প্রেমের দাঁত দেখেই জীবন কাটাবে। কোন ভালবাসাটা বেশি গভীর বলতে পারো?…তা মাইরি বউ যা একটা কথা বলল, সে আর পাবলিকলি বলতে পারব না। আজকালকার বউগুলো ব্যালেস্টিক মিসাইলের মতন দূর থেকে একেবারে জায়গা মতন হিট করে।”
মন্মথ হেসে উঠল। গুহও।
গুহ বলল, “সত্যি প্রেম, তুই বাঘের খাঁচায় পড়েছিস! তোর জন্যে বড় দুঃখ হয়।”
প্রেমকিশোর বলল, “বাঘের খাঁচা, কুমিরের মুখ, নদীর দ—যা খুশি বল, তবে এ-জীবনে এমন প্যাঁচে আমি পড়িনি। লাইফ সম্পর্কে আমার ধারণাই পাল্টে যাচ্ছে। জীবন, জগৎ, প্রেম, স্ত্রীলোক, সবই অলীক। বেঁচে থাকা অনর্থক।”.
মন্মথ বলল, “তুই শালা ফিলজফার হয়ে যাচ্ছিস নাকি! হয়ে যা, যে রকম কেস তাতে ত্যাগী, যোগী এসব না হলে আর বাঁচবি না।”
কিছুক্ষণ এইসব চলল। চা এল তারপর।
চা খেতে খেতে প্রেমকিশোর বলল, “তোরা কিছু ভাবতে পারলি?”
বন্ধুরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। সিগারেট ফুঁকল।
শেষে গুহ বলল, “আমরা অনেক প্ল্যান করেছি; ভেবেছি; তার মধ্যে তিনটে প্ল্যান স্ট্যান্ড করছে। এর মধ্যে তোকে একটা বেছে নিতে হবে।”
প্রেমকিশোর বলল, “প্ল্যান তিনটে কী শুনি?’’
মন্মথ বলল, “প্রথম প্ল্যানটা তোর ত্রিশূল পর্বতে পালিয়ে যাবার মতন।”
“মানে?”
“মানে, তুই একদিন বাড়ি থেকে কেটে পড়। কোন খোঁজখবর বাড়িতে দিবি না। ইচ্ছে করলে কলকাতার বাইরে পালাতে পারিস ; কলকাতার বাইরে যেতে না চাস, কোনো হোটেলে কিংবা আমাদের কারও বাড়িতে থাকতে পারিস। আমাদের কারও বাড়িতে থাকলে আমাদের বউরা সন্দেহ করবে। কাজেই হোটেল ভাল।”
“তাতে কী হবে?”
“তোর শশিকলা ঘাবড়ে যাবে। সে একা বাড়িতে দুদিন থাকলেই বুঝতে পারবে, শশী ইজ দেয়ার, বাট কলা ইজ নট দেয়ার ; কলাহীন শশী মানে নো শশী। সপ্তাহখানেক তুই ডুব মেরে থাক শশীর বারোটা বেজে যাবে। তারপর আমরা কেউ তোর বউয়ের সঙ্গে দেখা করব ; বলব, প্রেম ত্রিশূল পর্বত থেকে লিখেছে, সে আর সংসার করবে না। এই টরচার সে সহ্য করতে রাজি নয়। আপনি যদি মশাই, চুক্তিপত্র লিখে দেন, প্রেমকে আর টরচার করবেন না, তাকে চব্বিশ ঘণ্টা আপনার সামনে দাঁত বের করে বসে থাকতে হবে না, স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনযাপন করবেন, তা হলে প্রেম ফিরতে পারে। নয়ত নয়।”
প্রেমকিশোর মন দিয়ে পরিকল্পনাটা শুনল। তারপর বলল, “এটা হবে না; শশী অত কাঁচা নয়। নেক্সট টাইম যখন বাড়ি ঢুকব, আমায় ফায়ার করে দেবে।…সেকেন্ড প্ল্যানটা বল, শুনি।”
গুহ বলল, “সেকেন্ড প্ল্যানটা আমার। আমি অত ন্যাকামি বুঝি না। আমার কথা হল স্ট্রেট ডিল, প্রত্যেক হাজবেন্ডের রাইট আছে স্ত্রীর সঙ্গে নর্মাল লাইফ এনজয় করা। তোকে প্রেম কড়া হতে হবে, সাহসী হতে হবে। তোর বউ যেই দাঁত বের করতে বলবে সঙ্গে সঙ্গে তুই টারজানের মতন লাফ মেরে বউয়ের ঘাড়ে গিয়ে পড়বি। পড়ে বউকে নিয়ে বিছানায় ধরাশায়ী হয়ে যাবি। যেখানে সেখানে বার কয়েক কামড়ে দিবি, জোরে কামড়াবি না বেটা প্রথমে, ধীরে কামড়াবি, তাতেও বাগ না মানলে আরও জোরে কামড়াবি। মানে বউকে তুই ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল স্ট্রেংথ দিয়ে জিতে নিবি। পুরুষমানুষের মতন চেঁচাবি শালা, চেঁচাবি, লাফাবি, জিনিসপত্র দু-চারটে ভাঙবি, একটু মাল টেনে নিবি, দেখবি তোর বউ কেঁচো হয়ে গেছে। নিজের বউয়ের উপর যে স্বামী তার রাইট এস্টাব্লিশ করতে পারে না—তার মরে যাওয়া ভাল। বুঝলি?”
প্রেমকিশোর গুহর কথা শুনতে শুনতে উত্তেজিত হয়ে উঠছিল, কিন্তু যখন তার মনে হল শশিকলার সঙ্গে তাকে টারজানের খেল খেলতে হবে—তখন সে ভয় পেয়ে গেল। করুণ কণ্ঠে বলল, “না ভাই, ও আমি পারব না। আমি রোগাসোগা লোক, টারজান হতে গিয়ে বুকের হাড় ভাঙবে, পিঠের মাসল-এ খিচ লেগে যাবে, না হয় হাতের হাড় সরে যাবে, তারপর শালা বিছানায় শুয়ে ককিয়ে মরি আর শশিকলা আমায় অনবরত খোঁচাক। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা। না ভাই, আমি পারব না।”
প্রেমকিশোর সামনের সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট টেনে নিয়ে ধরাল। জিজ্ঞেস করল, “থার্ড প্ল্যানটা কী?”
এই প্ল্যানটা সুবীরের। কাজেই সুবীরকে বলতে হল।
সুবীর বলল, “তুই আগের দুটোতেই রাজি হচ্ছিস না, শেষেরটা কি পারবি?”
“শুনি।”
সুবীর বলল, “আমি অনেক ভেবে দেখলাম তোকে দাঁত তুলে ফেলতে হবে।”
প্রেমকিশোর হেঁচকি তোলার মতন শুরু করল, আসলে শব্দটা ভয়ের, শব্দ করে নিজের গালে হাত দিল। বলল, “দাঁত তুলে ফেলতে হবে, মানে?”
“মানে তোর নিজের কোন দাঁত থাকবে না। যদি তোর নিজের দাঁত না থাকে তবে আর তোকে নিয়ে কিসের রিসার্চ করবে? ফলস দাঁত তো আসল দাঁত নয় যে তার নিজের কিছু থাকবে। ঠিক কী না বল? ফলস চোখে দেখা যায় না, ফলস হাতে ধরা যায় না। মেয়েদের বাচ্চা হবার সময় ফলস পেইনে বাচ্চা হয় না। তোর দাঁত ফলস হলে শশিকলাও রিসার্চ ছেড়ে দেবে।”
প্রেমকিশোর খুব মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনতে লাগল এবং ভাবতে লাগল।
সুবীর বলল, “আমার এক বড় শালা ডেন্টিস্ট। ধর্মতলায় বসে। তার সঙ্গে কথা বলতে পারি। তবে বত্রিশটা দাঁত তো একদিনেই ভোলা যাবে না। মাস দুই অন্তত সময় লাগবে। তারপর বাঁধানো দাঁত করতে আরও হপ্তা তিন। এই তিন মাস তোকে কষ্ট সহ্য করতে হবে।”
প্রেমকিশোর গালে হাত রেখে বলল, “তোর কী মাথা খারাপ! তিন মাস আমি বাড়িতে সামাল দেব কী করে? তা ছাড়া আমার এই শক্ত শক্ত দাঁতগুলো চড়চড় করে টেনে তুলবে, উরে বাব্বা মরেই যাব! গলগল করে রক্ত বেরুবে, ব্যথায় প্রাণ যাবে, গাল ফুলে থাকবে। আমি এসবের মধ্যে নেই।”
সুবীর বলল, “তোর দাঁত কিন্তু যা বাঁধিয়ে দেব দেখবি।”
“নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভঙ্গ! সরি, আমি নাক কাটতে পারব না।”
সুবীর বলল, “ভালো করে ভেবে দেখ। যদি রাজি থাকিস, তোর ওই ভাঙা দাঁত দিয়েই নেক্সট উইক থেকে শুরু হতে পারে।”
প্রেমকিশোর জোরে জোরে মাথা নাড়ল।
গুহ বলল, “ব্যাপারটা পেইনফুল ; কিন্তু সুবীরের থিয়োরিটা কারেক্ট। ফলস দাঁত থাকলে শশিকলা তোর দাঁত দেখে একটি বর্ণও তোর রিঅ্যাকশন বুঝবে না। ঠাণ্ডা মেরে যাবে। আমার বউয়ের একবার ফলস হয়ে হয়েছিল।…”
হঠাৎ প্রেমকিশোর লাফ মেরে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়েই খেপার মতন বলল, “হয়েছে, হয়েছে! শালা হয়েছে! ইউরেকা! ইউরেকা!” বলে প্রেমকিশোর ঘরের মধ্যে চরকিপাক খেয়ে মাথার ওপর হাত তুলে নাচতে লাগল।
বন্ধুরা থ’ মেরে বসে রইল। হাঁ করে, অবাক হয়ে।
নাচতে নাচতে প্রেমকিশোর হাসতে লাগল, হাসতে হাসতে সুবীরের গলা জড়িয়ে পটাস করে দুটো চুমু খেয়ে ফেলল। বলল, “মার দিয়া! সাবাস সুবীর। শালা তুই গুরু লোক। আয়, তোকে একটা প্রণাম করি।”
প্রেমকিশোর আর দাঁড়াল না। হাত তুলে বন্ধুদের বলল, “চলি ভাই, কর্ম ফতে করে তবে ফিরব।”
“তোর হল কী? হঠাৎ খেপে গেলি কেন?”
“সে পরে শুনবি। আমি চললাম।”
“ব্যাপারটা বলে যা—।”
“এখন নয়। পরে। বাই বাই। “ নাচতে নাচতে প্রেমকিশোর চলে গেল। বন্ধুরা বোবা হয়ে বসে থাকল।
গুহ বলল, “বেটা কী দাঁত তোলাতে গেল নাকি?”
“মনে তো হয় না।”
“তবে?”
সুবীর, মন্মথ, গুহ কেউ কোন কিছু বুঝল না। অনুমান করতেও পারল না। চুপ করে বসে থাকল।
পাঁচ
বাড়িতে ঢোকার আগে প্রেমকিশোর কাছাকাছি বার-এ গিয়ে অল্প হুইস্কি খেয়ে নিল। তার সঙ্গে স্যারিডন। হুইস্কি তাকে মেজাজ দেবে ; আর স্যারিডন দাঁতের ব্যথা মারবে।
অন্যদিন প্রেমকিশোর চোরের মতন বাড়ি ঢোকে ; আজ বড় বড় পা ফেলে শব্দ করতে করতে ঘরে ঢুকল। শশিকলা ঘরে বসে বই পড়ছিল, প্রেমকিশোরকে হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকতে দেখে চোখ তুলে অবাক হয়ে তাকাল। তার পরনে মেয়ে প্যান্ট, গায়ে কামিজ।
প্রেমকিশোর বউয়ের দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসল।
শশিকলা বলল, “কী হয়েছে? উতনা হাসছ কেন?”
প্রেমকিশোর বলল, “রাস্তায় একটা লোক বাংলা খেয়ে খেমটা নাচছে।”
“খেমটা কী?”
প্রেমকিশোর অক্লেশে কোমরে হাত দিয়ে খেমটা নাচ দেখাল।
শশিকলা নাক মুখ কুঁচকে ধমক দিয়ে বলল, “স্টপ। ইয়ে ভালগার হ্যায়।”
প্রেমকিশোর কোমর থেকে হাত নামিয়ে বলল, “তোমাদের ইয়ে ঘুরিয়ে নাচ আরও ভালগার।”
“কোথায় গিয়েছিলে জি?”
“ডেন্টিস্টের কাছে।”
“কাল ভি গিয়েছিলে!”
“আজও গিয়েছিলাম। দাঁত ব্যথা করছিল। ওষুধ খেয়েছি।” প্রেমকিশোর হুইস্কি খাওয়াটা মেরে রাখল।
শশিকলা হাতের বই নামিয়ে রাখল। —“খানা খাবে?”
“খাব! রুটি, তরকারি, মাছ—সব খাব।”
“মাগর তোমার দাঁতে পেইন আছে।”
“গোলি মারো।”
শশিকলা ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। সন্দেহের চোখে স্বামীকে দেখল।
প্রেমকিশোর গ্রাহ্য করল না। আপন মনে প্যান্ট জামা খুলতে খুলতে হঠাৎ গান গাইতে লাগল : আমি ভয় করব না।
শশিকলা চমকে গিয়ে বলল, “সিঙ্গিং?”
“ও ইয়েস।”
“কেয়া হুয়া তোমারা জি?”
“ফিলিং ফাইন আফটার দি মেডিসিন।”
শশিকলা তাকিয়ে থাকল। প্রেমকিশোর গান গাইতে গাইতে বীরবিক্রমে বাথরুমে চলে গেল।
খেতে খেতে প্রেমকিশোর বলল, “দাঁত দেখাব?”
“নট নাউ।”
“ও-কে।…দাও রুটি দাও ; তরকারি দাও। কি মাছ, চিংড়ি? লাগাও, শালা সব খাব আজ।”
শশিকলা এবার ভয়ে ভয়ে প্রেমকিশোরকে দেখল। —“তোমার দেমাক খারাপ হয়ে গেছে জি।”
‘কুছ পরোয়া নেই। তুমি যখন আছ মাথা নিয়ে ভাবি না, ঠিক করে দেবে। সাইকোলজিস্ট বউ, হোয়াই শুড আই ফিয়ার!”
শশিকলার জন্যে অপেক্ষা করল না প্রেমকিশোরকে, নিজেই টেনে টেনে খাবার নিতে লাগল। শশিকলা বলল, “ডক্টর তোমায় কী ওষুধ দিয়েছে?”
“জানি না। ব্রান্ডি টাইপের গন্ধ ছিল।”
“হোয়াই ব্রান্ডি?”
“ডাক্তার জানে। আমি ডাক্তার নই।”
“ওহি বাস্তে তোমারা এতনা ফুর্তি…।”
“তোমায় বড় ভাল লাগছে। এই ড্রেসটা পরে থাকবে না ছাড়বে?”
“তুমি লুজ টক করছ।”
“তোমাকে লুজ করব।”
শশিকলা রেগে মেগে আর কথা বলল না।
শুতে এসে প্রেমকিশোর বেশ মেজাজের মাথায় সিগারেট খাচ্ছিল।
শশিকলা এল বেশ কিছুটা পরে। শাড়ি পরে শুতে পারে না শশিকলা। সিলোনিজ সায়ার মতন একটা বড়-সড় মাপের পেটিকোট পরে, সেটা অনেকটা ঘাঘরার মতন। গায়ে ঢিলেঢালা ব্লাউজ।
বিছানায় শুয়ে শশিকলা বলল, “বাত্তি বুজাও।”
প্রেমকিশোর বলল, “তুমি হিন্দি ছাড়বে না ছাড়বে না? বাঙালি মেয়ে তুমি। হিন্দি যতই বল, ভাল লাগে না।”
শশিকলা বলল, “বেশ।”
“বেশ মানে?”
“বেশ মানে বেশ, হিন্দি বলব না।”
“খুশি হলাম।”
শশিকলা গা-হাত ঝেড়ে গুছিয়ে শুল।
প্রেমকিশোর শশীর দিকে ফিরল। বলল, “তুমি চুলে কি মাখো?”
“কুছ না।”
“ফাইন গন্ধ দিচ্ছে।”
“শ্যাম্পুর গন্ধ।”
“বিউটিফুল। তোমার বডি পাউডারটা মার্ভেলাস।”
“তোমার আজ কী হয়েছে কী? এতনা বকবক করছ? কিতনা ব্র্যান্ডি খেয়েছ?” মনে মনে প্রেমকিশোর হাসল। শালা এক পেগ বড় হুইস্কিতেই এই কর্ম।
বলল, “বেশি নয়।”
“বাত্তি নেভাও।”
“বাত্তি নয়, বাতি—” বলে প্রেমকিশোর সোজা তার ডান হাত বউয়ের গায়ে চাপিয়ে দিল। ফুলশয্যার দিন হাত বাড়ানোর চেষ্টাও করতে পারেনি, ধমক খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল।
শশিকলা চমকে উঠে হাত সরিয়ে দেবার চেষ্টা করল। —“ই কেয়া?”
প্রেমকিশোর বলল, “বাংলায় একে আলিঙ্গন বলে ভাই, আলিঙ্গন জানো না?”
“হাত উঠাও।”
“নেভার।”
“ইউ মাস্ট।”
“নেভার, নেভার, নেভার…” বলতে বলতে প্রেমকিশোর হাত নামিয়ে শশিকলার পেটের কাছে সুড়সুড়ি দিল।
শশিকলা ছিটকে যাবার চেষ্টা করল, পারল না। প্রেমকিশোরের হাত উঠিয়ে দেবার জন্যে ধাক্কা মারল, পারল না।
প্রেমকিশোর এবার দু’হাত দিয়ে সুড়সুড়ি দিতে লাগল কোমরে আর পেটে।
শশিকলা শরীর ভেঙে দুমড়ে বেঁকে ক্ষণে ক্ষণে বিচিত্র আকার ধরতে লাগল। এবং সে হাসতে লাগল।
প্রেমকিশোর বিছানার ওপর উঠে বসে কীচক বধের ভঙ্গি করে শশিকলার সর্বাঙ্গে সুড়সুড়ি দিতে লাগল।
শেষ পর্যন্ত শশিকলা বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে মাটিতে নামল। প্রেমকিশোরও লাফ মারল। ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি। শশিকলার ঘাঘা পেখম মেলে নাচছে, হাত কখনো বুকের কাছে, কখনো মুখের কাছে। আর প্রেমকিশোর শশিকলার সামনে কোমর ভেঙে ফ্রি স্টাইল কুস্তির ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে রয়েছে সুড়িসুড়ি দেবার জন্যে। “প্লিজ প্রেম”—
“নেভার।”
“আমি বেশি হাসতে পারি না।”
“কেন পারো না। হাসি ভাল। হাসলে আয়ু বাড়ে, চর্বি ঝরে যায়।”
“আমার চর্বি নেই প্রেম।”
“ভয়ঙ্কর চর্বি তোমার। মেন্টাল চর্বি।” বলতে বলতে প্রেমকিশোর আবার ধরে ফেলল শশিকলাকে। শশিকলার গলার স্বর মোটা হয়ে গিয়েছে, মোটা গলায় হাসতে লাগল, যেন জলভরা বোতল থেকে জল পড়ছে।
তারপর সারা ঘর লণ্ডভণ্ড। শশিকলা লাফ মেরে বিছানায় উঠল। প্রেমকিশোর লাফ মারল। শশিকলা মাথার দিকে পালাল বিছানার—প্রেমকিশোর পাশ থেকে গিয়ে জাপটে ধরল।
হাসতে হাসতে বসে পড়ল শশিকলা। প্রেমকিশোর দাঁড়িয়ে থাকল। শশিকলা এবার পালাবার চেষ্টা করল। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে ছুটল।
দরজার ছিটকিনিতে হাত দিতেই পারেনি শশিকলা—প্রেমকিশোর এসে জাপটে ধরল।
কোমরের দু’পাশে হাত রেখে জোর কাতুকুতু দিতেই শশিকলা এত জোরে হেসে উঠল যে কি যেন তার মুখ দিয়ে ছিটকে বেরিয়ে দরজায় খট করে লাগল। লেগে মাটিতে পড়ল। শশিকলা একেবারে থ।
প্রেমকিশোর দেখল, দাঁতের বাঁধানো পাটি, পুরো পাটি।
শশিকলা তাকাল প্রেমকিশোরের দিকে। চোখে মুখে ধিক্কার, দুঃখ, বেদনা, ধরা পড়ে যাবার ভয়, লজ্জা।
প্রেমকিশোর মাটি থেকে দাঁতের পাটিটা কুড়িয়ে নিল। নিয়ে ডান হাত পাতল।
শশিকলার চোখে জল এল। মুখ থেকে অন্য দাঁতের পার্টিটা বের করে প্রেমকিশোরের হাতে দিল।
ছত্রিশ বছরের শশিকলার ভরন্ত মুখ চুপসে গেল। যেন কেউ পিন ফুটিয়ে বেলুন চুপসে দিয়েছে। হঠাৎ শশিকলা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।
প্রেমকিশোর দাঁতের পাটি দুটো বিছানার দিকে ছুড়ে দিল। বলল, “কেঁদো না। প্লিজ।”
শশিকলা আরও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।
প্রেমকিশোর শশিকলার হাত ধরে টানতে টানতে বিছানায় এনে বসাল। বলল, “তুমি রোজ রাত্রে, আমি ঘুমিয়ে পড়ার পর দাঁতের পাটি দুটো বালিশের তলায় লুকিয়ে রাখতে?”
মাথা নাড়ল শশিকলা। হ্যাঁ, রাখত।
প্রেমকিশোর বলল, “আবার ভোরে উঠে পরে নিয়ে বাথরুমে যেতে?”
এবারও স্বীকার করল শশিকলা।
“আমায় বরাবর ফলস দিচ্ছিলে?”
শশিকলা চুপ।
“তোমার দাঁত ফলস বলে তার কোনো ফিলিং ছিল না।”
শশিকলা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।
প্রেমকিশোর একটু হাসল। হাত দিয়ে শশিকলার চোখের জল মুছিয়ে দিতে গিয়ে সারা গাল লেপটে দিল। তারপর বলল, “তোমাকে এখন আরও বিউটিফুল দেখাচ্ছে। আই ডোন্ট কেয়ার ফর দোজ ফলস…। এসো, শুয়ে পড়ো।”
প্রেমকিশোর শশিকলাকে শুইয়ে দিয়ে নিজে পাশে শুয়ে পড়ল।
বেড সুইচ টিপে বাতি নেভাল। তারপর শশিকলার দিকে ফিরে তাকে জাপটে নিয়ে বলল, “ডার্লিং, তুমি মন খারাপ করো না। তোমার নিজের দাঁত না থাক—আমার আছে। আমি, তোমার কাজ চালিয়ে দেব। কই, মুখটা দেখি…। তোমার মুখে মার্ভেলাস গন্ধ।…শশী, এসো ভাই লক্ষ্মীটি…” বলতে বলতে প্রেমকিশোর এমন জোর একটা চুমু খেল বউকে—মনে হল নতুন টিউবওয়েলে জল তুলছে।
ফণীমনসা
মনোবীণা গিয়েছিলেন তীর্থ করতে। তীর্থ মানে হরিদ্বার হৃষীকেশ ঘুরে আসতে। গিয়েছিলেন বন্ধু হালদারের দলের সঙ্গে। বাড়ি ফিরে যা দেখলেন তাতে ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠার অবস্থা।
মনোবীণার কর্তা ফণীশ্বর শোবার ঘরে দড়ির জালের দোলনা—যাকে কিনা হ্যামক বলে—সেইরকম এক দড়ি-দোলনা ঝুলিয়ে তার মধ্যে শুয়ে আছেন। তিন চারটে গোল লম্বা বালিশ বা কুশন তাঁর দেহের এ-পাশে ও-পাশে, মাথায়। বাঁ হাতে প্লাস্টার, ডান পায়ে প্লাস্টার। পরনে লুঙ্গি, গায়ে বেঢপ ফতুয়া। ফণীশ্বরের ডান হাতের কাছে এক ফিডিং বটল, আজকাল যেমনটি দেখা যায়—সেই ছাঁদের।
মনোবীণা তীর্থ সেরে এসেছেন। তীর্থ সেরে এসে তাঁর ডাকসাইটে শাশুড়ি সদরে দাঁড়িয়ে তিন ঘটি জল পায়ে ঢেলে তবে বাড়ির মধ্যে ঢুকতেন। মনোবীণা দেখেছেন।
গাড়ি থেকে নামতেই পারুল আর খেঁদা ছুটে এসে যে-খবর শোনাল—তাতে আর মনোবীণার পায়ে জল ঢালার সময় হল না। ক’দিনের ঘোরাঘুরি হাঁটাহাঁটিতে এমনিতেই তাঁর পা ফুলেছে, ব্যথা ; তবু সেই ফোলা পায়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সোজা দোতলায়। শোবার ঘরে।
ঘরে ঢুকে দেখেন স্বামী দোলনায় শুয়ে, ডান হাতে দুধ-বোতল। কর্তা ছাদের দিকে চোখ তুলে শুয়ে গান গাইছেন, ব্রহ্মসঙ্গীত।
“ওমা! কী হয়েছে? এ কী দশা তোমার?” বলতে বলতে মনোবীণা স্বামীর দোলনার পাশে এসে ঝুঁকে পড়লেন। এমন করে ঝুঁকলেন যেন কর্তার বুকের ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়বেন।
ফণীশ্বর যেহেতু ব্ৰহ্মসঙ্গীত গাইছিলেন, ‘হৃদয় আরাম তুমি হৃদয়নাথ’ সেহেতু আধবোজা চোখে, আধ্যাত্মিক আবেশের গলায় বললেন, “পতিত হয়েছি।”
মনোবীণা একে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত তার ওপর বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতেই স্বামী-দুঃসংবাদে আতঙ্ক-উৎকণ্ঠায় দিশেহারা, কাজেই স্বামীর ওই মিনমিনে আধ্যাত্মিক গলা ভাল লাগল না ।বললেন, “আদিখ্যেতা রাখো। কী হয়েছিল? কেমন করে পড়ে গেলে?”
ফণীশ্বর বললেন, “তোমার তেলের শিশিতে।…তেলের শিশি ভাঙল বলে—।”
মনোবীণা অবাক। আজ পনেরো দিনের বেশি তিনি বাড়ি-ছাড়া, তাঁর তেলের শিশিতে কর্তার আছাড় খাবার কী হল?
গায়ের পাতলা চাদরটা খুলে একপাশে ছুড়ে দিতে দিতে মনোবীণা বললেন, “আমি রইলুম হাজার মাইল দূরে, আমার তেলের শিশিতে তুমি আছাড় খেলে? তামাশা।”
“তামাশা কেন হবে! যা হয়েছে তাই বললাম। ”
“কখনওই নয়। আমি বিশ্বাস করি না। কত খেয়েছিলে তখন—পেট পর্যন্ত, না, গলা পর্যন্ত?”
ফণীশ্বর তখনও শান্ত গম্ভীর গলায় বললেন, “সেদিন পূর্ণযোগ ছিল না, ফকির চেটো—মানে চাটুজ্যের মা উননব্বইতে স্বর্গ গেলেন ; আমরা বন্ধুর মাতৃশোক জানাতে অর্ধযোগ সেরেই ফিরে এসেছিলাম। বীণা, স্বামীকে বিশ্বাস করা তোমার পবিত্র কর্ম।”
মনোবীণার মাথা গরম হয়ে উঠেছিল। এই ন্যাকামি আর সহ্য হচ্ছিল না। রাগের মাথায় দোলনাটা ঠেলে দিলেন। দোলনা সামান্য দুলতে লাগল। বললেন, “নিকুচি করেছে তোমার পবিত্তর কম্মে। ঠিক ঠিক বলল কী হয়েছিল। আমার তেলের শিশি থাকে কলঘরে। সেই শিশি উড়ে এসে তোমার পায়ে পড়ল! তার পাখা গজিয়েছিল নাকি?”
ফণীশ্বর কী বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই বীণা ধমকে উঠে বললেন, “ঢং করে কথা বলবে না। সাফ সাফ বলো। সাদা কথায় বলো।”
“ভেতো বাংলায়?”
“হ্যাঁ।”
ফণীশ্বর বললেন, “তা হলে যা যা ঘটেছিল বলি। একটিও মিথ্যে কথা বলছি না, ধর্ম সাক্ষী। …সেদিন বিকেলে চাটুজ্যের মায়ের গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটল! আমরা চেটোকে বললাম, তুমি শ্মশানে যাবে—লোকজন তোমার অঢেল, রাবণের ফ্যামিলি, আমরা আর বোঝার আঁটি হয়ে কী করব! তার চেয়ে বরং একটু শোক পান করে বাড়ি ফিরে যাই। চেটো এক পাত্তর টেনে চলে গেল। বড় দুঃখ তার। মা বলে কথা। হোক না নব্বইয়ের গোড়ায়। আমি, দ্বিজু, গণেশ খেলাম খানিকটা, পুরো খাইনি। অর্ধযোগ। তারপর যে যার বাড়ি।… বাড়ি ফিরে এসে বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। তুমি নেই। তুমি না থাকলে আমি একেবারে অনাথ শিশু। অরফ্যান—”, বলতে বলতে ফণীশ্বর একটু থামলেন। গলা পরিষ্কার করে নিয়ে আবার বললেন, “ভাবলাম, একটু শুদ্ধ হয়ে নিই চান করে। হাজার হোক চেটোর বাড়ি থেকে ফিরছি। সংস্কার বলে একটা কথা আছে তো!… তা ইয়ে, মানে তোমার অভাবে তোমারই মাথার তেল—জবাকুসুম মাথায় ঘষতে ঘষতে পায়চারি করছিলাম এখানেই। সাম হাউ, হাত ফসকে শিশিটা পড়ে গেল। অ্যান্ড ব্রোকেন…। আমিও তেলের মেঝেতে পা হড়কে পড়লাম। জবর পড়লাম গো! অ্যান্ড ব্রোকেন..!”।
“বেশ হয়েছে।”
“বেশ হয়েছে। আমার হাত ভাঙল, পা ভাঙল—আর তুমি বলছ বেশ হয়েছে। তোমার বাক্য শুনে…।”
“তোমার মাথাটা ভাঙল না কেন!” বলে মনোবীণা স্বামীর হাতটা দেখতে লাগলেন, “গোটা হাতটাই ভেঙেছে?”
“কবজির ওপরটা দুটুকরো…”
“চমৎকার। চার হল না কেন? …আর পা? দেখি পা দেখি।”
ফণীশ্বরের কপাল ভাল গোড়ালির তলার দিকে হাড় পুরোপুরি না ভাঙলেও চিড় ধরেছে। প্লাস্টার করা আছে পা, প্রায় হাঁটুর কাছাকাছি পর্যন্ত।
পা দেখতে দেখতে মনোবীণা বললেন, “ছেলেকে খবর দিয়েছিলে?”
“দিয়েছিলাম। খোকা বউ নিয়ে ছুটতে ছুটতে এল মোটর বাইক হাঁকিয়ে। ওদের কারখানায় হুজ্জোতি চলছে। প্লাস্টার হয়ে যাবার পর আমিই ওদের বললাম, তোরা যা, এসময় কারখানা ছেড়ে থাকিস না।”
“ওরাও চলে গেল? মানুষ, না জন্তু?”
‘আহা, গালাগাল দিচ্ছ কেন! ছেলে আর বউমার দোষ কোথায়? আমি বললাম বলেই ওরা চলে গেল। খোকার কারখানায় ভীষণ ঝামেলা চলছে না! গো স্লো, মিটিং, লাঠালাঠি, পুলিশ—যা হয় আজকাল। খোকার কোয়ার্টারটাও বেমক্কা জায়গায়। এ সময় নিজের কোয়ার্টার আর কারখানা ছেড়ে আসতে নেই।”
মনোবীণ খুশি হলেন না। গরমকালের বাঁধাকপির মতন বিদিকিচ্ছিরি মুখ করে বললেন, “খোকার বউ কী করছিল? সে কোন আক্কেলে বুড়ো হাত-পা ভাঙা শ্বশুরকে ফেলে রেখে চলে গেল?”
ফণীশ্বর বললেন, “দুঃসময়ে স্ত্রীকে পাশে থাকতে হয়। সীতা রামকে ফলো করেছিল কেন?”
“চুলোয় যাক তোমার সীতা!… খোকাকেও বলিহারি। তোর বুড়ো বাপ থাকল পা-ভেঙে পড়ে, তুই বেহায়ার মতন বউ ট্যাঁকে করে পালালি! ছি ছি, আজকালকার ছেলেমেয়েদের লজ্জা শরম, কর্তব্য জ্ঞান বলে কিছু নেই!”
ফণীশ্বর গম্ভীর হয়ে বললেন, “আগেও ছিল না!”
“ছিল না? আমরা হলে এ কাজ করতে পারতাম?”
“চমৎকার পারতাম। এই ধরো, তোমার-আমার কথা। তখন আমাদের মাত্তর পাঁচ মাস বিয়ে হয়েছে। বাবার টাইফয়েড হল। পানাগড়ে। খবর পেয়ে আমরা ছুটে গেলাম। দিন আষ্টেকের মাথায় বাবা যখন টাল সামলেছে—আমি চলে আসতে চাইলাম। তুমি তখন কী করলে? আমার লেংটি ধরলে। কিছুতেই বাবা-মায়ের কাছে থাকবে না, বললে—আমায় নিয়ে চলল, আমি একলা থাকতে পারব না। সে কী মুখ তোমার? কী কান্না!..কই, তখন তোমার লজ্জা-শরম কোথায় ছিল?”
মনোবীণা ধরাপড়া চোরের মতন মিইয়ে গিয়ে বললেন, “অমন জলজ্যান্ত মিথ্যে কথাটি বোলো না। বাবার মোটেই টাইফয়েড হয়নি। জঙ্গল ম্যালেরিয়া হয়েছিল। বাবা তখন সেরে উঠেছেন। মা বললেন বউমা—তুমি যাও, ছেলে একা থাকে—রাত-বিরেতে চাকরি। তুমি না থাকলে ওর অসুবিধে হবে।”
“মা বললেন—”আর তুমি আমার কাছাটি ধরে সুড়সুড় করে চলে এলে! কী আমার শাশুড়ি-ভক্তি।”
‘কাঁচা তোমার ছিল যে ধরব! করতে তো এ টি এস-এর কাজ, পরতে খাকি হাফ প্যান্ট…, ধরতে হলে ওই পেন্টুল ধরে টানতে হত।” বলতে বলতে বীণা দেওয়ালের পুবদিকে তাকালেন। শাশুড়ির বড় ফটো। জাঁদরেল মহিলা ছিলেন। হাত জোড় করে বার কয়েক প্রণাম সেরে ফেললেন স্বর্গ শাশুড়ির উদ্দেশে, তারপর মুখ ঘুরিয়ে পশ্চিমের দেওয়ালে শ্বশুরমশাইয়ের ফটোকেও প্রণাম জানালেন। তীর্থ সেরে ফিরে এসেছেন সবে, গুরুজনরা সশরীরে বর্তমান থাকলে ঘটির জলে পা ধুইয়ে দিয়ে প্রণাম করতেন। তা যখন নেই, তখন তো নমো নমো করতেই হয়।
ফণীশ্বর এবার দুধ-বোতল মুখে তুললেন।
মনোবীণা বললেন, “ওটা কী? খোকা হয়েছ?”
ফণীশ্বর বললেন, “টু ইজটু থ্রি প্রপোরশানে মেশানো আছে। দুই তিন ভাগাভাগি।”
“গন্ধতেই বুঝতে পারছি কী মেশানো আছে।”
ডাবের জল আর ইয়ে—মানে এক নম্বর দিশি।”
“দিশি! দিশি…।”
“ডাক্তার বলল আমি কী করব! বলল, বিলিতি রাত্তিরে খেয়ো, সারাদিন খেলে সইবে না। তার চেয়ে ডাবের জলের সঙ্গে লোকাল মিশিয়ে খেলে গরমে তেষ্টা মিটবে, গায়ে-হাতের ব্যথা মরবে। ফুরফুরে হয়ে থাকতে পারব—তাই!”
“তাই! তাই খোকাপনা ধরেছ!”
‘না, না, তার জন্যে কেন হবে! দোলনায় দুলে দুলে খাই তো, হাত ভাঙা মানুষ, ধরতে সুবিধে। আমি তো আর বোঁটা চুষি না! ওটা খুলে রেখেছি।”
মনোবীণা স্বামীকে বিলক্ষণ চেনেন। পঁয়ত্রিশ বছর ধরে সমানে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিল মানুষটা। বললেন, “এটাও কি ডাক্তারে বলেছে?”
“মাপ! মাপ পাব কোথায়! এখানে শিশির গায়ে মাপের দাগ আছে, ওয়ান আউন্স টু আউন্স—! কত সুবিধে!”
“কে দেখেছে তোমাকে কোন ডাক্তার?”
“সরোজ।”
“সরোজিনী! সরোজিনী তোমাকে দেখেছে! ও তো মেয়ে ডাক্তার!” বীণার যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না। বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকলেন।
ফণীশ্বর বেশ গম্ভীর এবং আবেগের গলাতেই বললেন, “সরোজ না থাকলে সেদিন হাড়ভাঙা দ হয়ে পড়ে থাকর্তাম। খবর পেয়েই ছুটতে ছুটতে এল। তারপর যা করার সেই করছে। শুধু প্লাস্টারটা করে দিয়েছে মানিক মুখুজ্যে।”
সরোজিনী থাকেন কাছেই। দু’চার বাড়ির পরই। একটু কোনাচে জায়গায় বাড়িটা। পেশায় ডাক্তার। রেল হাসপাতালের। মহিলার চেহারা দেখলে পুরুষ বলে ভুল হতে পারে। মাথায় বেঁটে, রং কালো, বহর বিশাল, সামান্য গোঁফ আছে নাকের তলায়, সপ্তাহে বার দুই মিহি করে গোঁফ পরিষ্কার করে নেন ইলেকট্রিক রেজারে। মেজাজ অতি উগ্র। চোখে বড় বড় কাচের চশমা, মাথার চুল কাঁচা-পাকা, ঘাড় পর্যন্ত চুল। সরোজিনী হলেন মিস, মানে বাহান্ন-তিপান্ন বছর বয়েসেও কুমারী।।
মনোবীণার ইচ্ছে হল, শুয়ে পড়ে মেঝেতে মাথা ঠোকেন কিছুক্ষণ! শহরে এত ডাক্তার বদ্যি থাকতে শেষে নাকি ওই ‘মা মনসা’!মনোবীণা আড়ালে সরোজিনীকে মা মনসা বলেন। পাশাপাশি বাড়ি, (যদিও মা মনসার হল ভাড়া বাড়ি) আলাপ পরিচয় আছে বইকি! কিন্তু মেলামেশা তেমন নেই। মনসা মদ্দ নয়, মাগি ; ও সিগারেট খায় বলে শুনেছেন মনোবীণা, এমন কি বাড়ির মধ্যে রাত্রে ঢুকুঢুকুও চলে!
“তুমি শেষ পর্যন্ত মনসার খবরদারিতে আছ, ছিছি!”
“সরোজ ভাল ডাক্তার। গোল্ড মেডেল পেয়েছিল।”
“ও তো মেয়েদের ডাক্তার!”
“তা বলে গাইনি নয়। জেনারেল ফিজিশিয়ান, প্লাস কার্ডিওলজিস্ট!”
“নিকুচি করেছে অমন ডাক্তারে। আসলে তোমার ধাতটি ও বোঝে তো! রতনে রতন চেনে। তাই ফিডিং বোতলে মদ ঢেলে খেতে বলে গেছে! ঘেন্নায় মরি।”
ফণীশ্বর যেন কত কৃতজ্ঞ সরোজিনীর কাছে, মুক্তকণ্ঠে বললেন, “এই দোলনাটিও ও নিজের বাড়ি থেকে এনে টাঙিয়ে দিয়ে গেছে। বলেছে, জানলার কাছে নিচু করে টাঙিয়ে দিয়ে গেলাম। শুয়ে শুয়ে সব দেখবেন শুনবেন, ভাল লাগবে। দিন কেটে যাবে।”
মনোবীণা বললেন, “তা হলে আর কী! ওই দোলনায় শুয়ে শুয়ে দোলো! ঢং যত্ত।”
দুই
আর খানিকটা বেলায় স্বামীকে এমন করে স্নান করিয়ে দিলেন মনোবীণা যেন পনেরো দিনের ময়লা কলঘর সাফ করছেন। অবশ্য প্লাস্টার সামলে, যেন না জলে ভিজে যায়!
স্নানের পর স্বামীকে পোশাক পরিয়ে দিলেন। লুঙ্গি আর ঢোললা ফতুয়া। দিয়ে বললেন, “একটু বসো, আমি চান সেরে নিই!”
স্নান শেষে মনোবীণা পুজোর শাড়ি পরে খালি গায়ে স্বামীর কাছে এসে তীর্থ থেকে আনা প্রসাদী ফুল পাতা ছোঁয়ালেন তাঁর মাথায় বুকে। তারপর আঁচলের গিট খুলে কাগজে মোড়া একটা মাদুলি বার করলেন। বললেন, “পুজো দেওয়া শুদ্ধ করা মাদুলি। এটা পরো।”
“কেন?”
“আমি কোন মুলুক থেকে এনেছি ; ভৈরবচণ্ডীর মন্দিরে পুজো দিয়ে…”
“কী হবে পরে? পুজোই বা দিতে গেলে কেন?”
“এ খুব জাগ্রত। এতে কত কী হয়!”
“আমার আবার কী হবে! হবার দিন তো শেষ।”
“তোমার ওই নেশাটি আমি ছাড়াব! বয়েস এখন কত হল? পঁয়ষট্টি। সেই কোন বয়েস থেকে গেলাস ধরেছ! তবু যৌবনকালে সব সয়। এখন কি ওই সব সইয়ে নেওয়ার বয়েস আছে! বরং দিন দিন তুমি ইয়ার বন্ধুদের সঙ্গে বসে গেলাস গিলছ গাদা গাদা। শরীর তো যেতে বসেছে। লিভার পচে গেল।”
ফণীশ্বর স্ত্রীকে দেখতে দেখতে বললেন, “লিভার পচবে কেমন করে! সব সময় অ্যালকোহলে ডুবিয়ে রাখছি। তুমি জান, অ্যালকোহল হল বেস্ট জার্মিসাইডাল। বীজাণু নিরোধক : অ্যান্টি ব্যাকটিরিয়া প্রপার্টি রয়েছে ওতে। আমার লিভার…”
স্বামীকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বীণা কর্তার পিঠে এক ধমক-মারা কিল বসিয়ে দিলেন। রুক্ষ গলায় বললেন, “আমি পরতে বলছি, পরতে হবে। এর বেশি কথা নেই। আমি তোমার বউ, আমার কথাই শেষ কথা।”
কী ভেবে ফণীশ্বর একটু হাসলেন। তারপর বললেন, “বেশ। তোমার কথাই থাক। যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি।”
মনোবীণা স্বামীর হাতে মাদুলি বেঁধে দিলেন।
তিন
ফণীশ্বর যাকে ‘পতিত হওয়া’ বলেছিলেন সেই ঘটনাটি ঘটেছিল—গরমের মুখে, ফাল্গুন মাস নাগাদ। তারপর তিনটি মাস কেটে গেল। তিন মাসে হাত-পায়ের প্লাস্টার খোলা হয়ে গিয়েছে। পায়ের চোট এখনও সামান্য ভোগাচ্ছিল, যেমন ব্যথা, মাঝে মাঝে গাঁট ফোলা। হাত মোটামুটি কর্মক্ষম। বয়সের হাড়-ভাঙা, সহজে কি সারবে! বাত-টাত ধরবে বইকি।
এই তিন মাসে ফণীশ্বরের কিছু পরিবর্তন হয়েছে। বন্ধুদের আসরে যাওয়া কমেছে খানিকটা। আরও কমে আসছে ক্রমশ। সাইকেল রিকশা করে চেটোদের আড্ডাখানায় আসা যাওয়ায় বোধহয় অসুবিধে হয়। পায়ের জন্যেই হবে হয়তো। ফলে পানাদি অভ্যাস কমে আসছে। বাড়িতে তো মনোবীণা মেয়ে দারোগা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সর্বক্ষণ, কাজেই সুবিধে হয় না তেমন। তবে মনোবীণা তো অতিরকম নিষ্ঠুর নন, স্বামীর ধাত বোঝেন। মানুষটাকে তিনি ধীরে সুস্থে সামলাতে চান, সৎ পথে আনতে চান। এতকালের অভ্যেস দুম করে একদিনে ছাড়িয়ে দিতে তিনি চান না, তাতে ভীষণ ক্ষতি হবে। রয়ে সয়ে যা করার তেমন করাই ভাল। মানুষটার শরীর মনও তো দেখতে হবে।
ফণীশ্বর মদ্যমাত্রা বেশ কমিয়ে ফেলেছেন।
মনোবীণাও কত স্বস্তি পাচ্ছেন মনে মনে। আর দু’চার মাস পরে স্বামী একেবারে সাধু সন্ত হয়ে যাবেন।
বীণা যখনই সময় পান ফণীশ্বরের হাতে বাঁধা মাদুলিটি দেখেন প্রাণভরে, মনে মনে ভৈরবচণ্ডীকে প্রণাম জানান। ঠাকুর তুমি আমায় বাঁচালে। তোমার মতন জাগ্রত দেবী আর কে আছে। তা সেদিন সন্ধের মুখে মুখে ফণীশ্বর পাজামা পাঞ্জাবি চড়িয়ে নীচে নামতে যাচ্ছেন-—মনোবীণা বললেন “যাচ্ছ কোথায়?”
ফণীশ্বর বললেন, “এই কাছেই।”
“কোথায়?”
“এই তো— আশেপাশে। খেতে যাচ্ছি না আজ। শরীরটা বড় অলস হয়ে যাচ্ছে। একটু ঘোরা-ফেরা না করলে কী চলে!”
মনোবীণারও মনে হল, কর্তার আগে যেমন হাঁক ডাক ছিল—এখন তার অর্ধেক কমে গিয়েছে। গলার জোর কমতির দিকে। আগে সকালে বাজার যাবার সময় খেঁদাকে গোটা চারেক থলি নিতে বলতেন, এখন দুটোতেই চলে। বয়েস হলেও খাওয়া-দাওয়ায় রুচি ছিল খানিকটা ভোজনপটু ছিলেন ; অকারণ সাত রকম বাজার সেরে ফিরতেন। মিষ্টিমাস্টা তো বাঁধা ছিল। দু’দুটো করে রসগোল্লা একসঙ্গে মুখে ফেলতেন। মাছ মাংসও চলত সমানে। বীণা শত বলেও খাওয়া-দাওয়ায় সামলাতে পারতেন না তাকে। এখন সেই মানুষেরই বাজার কমেছে, খাওয়া কমেছে। দিন রাত বড় বেশি হাই তুলছেন। হালে কোথথেকে ঘেঁটেঘুটে একটা গীতা বার করেছেন। পাতা ওলটান রোজ।
ছেলে ছেলের বউ হপ্তায় একদিন করে আসে। শনিবার। রবিবার সন্ধেবেলায় আবার মোটর বাইক হাঁকিয়ে নিজের জায়গায় চলে যায়। খোকাও বলছিল, “মা, বাবাকে কেমন উইক উইক দেখাচ্ছে। খাওয়া-দাওয়া কমিয়ে দিয়েছে। তুমি কিছু বলছ না?”…ছেলের বউয়েরও একই কথা, “মা, বাবার শরীরটা কেমন ভেঙে আসছে।”
মনোবীণা ছেলে বা ছেলের বউকে কিছু বলেননি। ওকথা কি বলা যায়, আমি তোদের বাপকে নেশা ছাড়াবার জন্যে মাদুলি পরিয়েছি মানত করে। নেশাখোর মানুষ তো, নেশা ছাড়তে গিয়ে একটু-আধটু ন্যাতানো লাগতেই পারে। ও ঠিক হয়ে যাবে।
ফণীশ্বর পা বাড়াতে যাচ্ছেন, মনোবীণা বললেন, “বেরোেচ্ছই যখন—আরও খানিকটা আগে আগে বেরুলে পার। বিকেল বিকেল। সকালেও তো খানিকটা হেঁটে চলে আসতে পার!”
ফণীশ্বর বললেন, “সকালে উঠতে ইচ্ছে করে না। আমি তো হাঁস-মুরগি নই যে ভোর হল কি বেরিয়ে পড়ব!… আর বিকেল-বিকেল বেরুব কোথায়! যা ভ্যাপসা গরম!”
মনোবীণা আর কিছু বললেন না।
ফণীশ্বর বেরিয়ে গেলেন।
সন্ধের গোড়ায় গা ধুয়ে, এক কৌটো পাউডার গায়ে ছড়িয়ে, চুলের একটা আলগা ঝুটি বেঁধে মনোবীণা গেলেন ঠাকুরঘরে। ঠাকুরঘরে তিনি রোজই প্রদীপ জ্বালান। শাশুড়ির সেই প্রদীপটি এখনও তিনি মেজে ঘষে পরিষ্কার করেন নিজের হাতে। প্রদীপ জ্বালান। ঠাকুর নমস্কার করেন।
ঠাকুরঘর থেকে ফিরে নিজের ঘরে এসে জল পান খাচ্ছেন, এমন সময় বৃষ্টি এল।
‘ওরে খেঁদা, ওরে খেঁদা—বৃষ্টি এল দেখ দেখ— বলতে বলতে তিনি শোবার ঘরের বাইরে বারান্দায় আসতেই আচমকা চোখে পড়ল—একেবারে কোণাকুণি বাড়ির দোতলায় একটা ঘরের পরদা উড়ে যাচ্ছে বাতাসে, আর পরদার ফাঁক দিয়ে কাকে যেন দেখা গেল না? কর্তা! কর্তা—এই বাড়িতে না?
বৃষ্টির ছাঁট বাঁচাতে ঘরের দরজা জানলা বন্ধ হয়ে গেল বাড়িটার। আর কিছু দেখা গেল না।
মনোবীণা নিজের চোখকে বিশ্বাস করবেন? নাকি মাথাটাই গোলমাল হয়ে গেল? ওই বাড়িটা তো মা মনসার—মানে সরোজিনীর। কর্তা ওই বাড়িতে গিয়েছেন কেন? ওখানে কী দরকার তাঁর? আশ্চর্য তো!
চোখের ভুলও হতে পারে।
তা চোখের ভুল হোক না-হোক, ব্যাপারটা তাঁর পছন্দ হল না। ভাল লাগল না মোটেই। মন কেমন খুঁত খুঁত করতে লাগল।
আসুন কত বাড়ি ফিরে, তারপর দেখা যাবে!
ফণীশ্বর বাড়ি ফিরলেন আটটা নাগাদ।
মনোবীণা দেখলেন কর্তাকে। “কোথায় গিয়েছিলে?”
“এই তো! বৃষ্টি চলে এল।”
“সে সবাই জানে। তুমি কোথায় গিয়েছিলে!”
“এই তো—এদিকেই। কাছেই ছিলাম।”
“এই তো সেই তো রাখো! কোথায় গিয়েছিলে বলো?”
ফণীশ্বর গিন্নিকে দেখতে দেখতে বললেন, “হল কী তোমার?”
“তুমি ওই মা মনসার বাড়ি গিয়েছিলে?”
ফণীশ্বর একটু যেন থতমত খেলেন। “হ্যাঁ, একবার যেতে হল!”
“যেতে হল? কেন?”
“তেমন কিছু নয়।”
“তেমন-টেমন থাক। কেন গিয়েছিলে?”
ফণীশ্বর নিজের বুকটা দেখালেন। বললেন, “একটু ব্যথা-ব্যথা করে উঠল।”
“কী! মনসার জন্যে ব্যথা?”
“আরে না! কী যে বলো! হার্ট।… হার্টের এই পজিসনে— বাঁ দিকে ব্যথা-ব্যথা। বাঁ-হাতটাও ঝিনঝিন করে উঠল। তা ভাবলাম, যাই একবার সরোজকে দেখিয়ে নিই।”
“মনসাকে তোমার বুকের ব্যথা দেখাতে গেলে?”
“বাঃ! সরোজ ভাল কার্ডিওলজিস্ট। সে আমাকে গত তিন চার মাস ধরে দেখছে। ওর কাছে, মানে বাড়িতেই যত্তর আছে। পটাপট ইসিজি করে ফেলে।”
মনোবীণার মাথায় যেন রক্ত চড়ে গেল, “ও, তুমি বুড়ো—ওই মনসার বাড়িতে গিয়ে জামা খুলে বিছানায় শুয়ে পড়লে!”
“বিছানা! হায় প্রভু! বিছানা! চওড়া সোফা—সোফা, লম্বা সোফা। টেবিল তো একতলায়। সেখানে গিয়ে শুতে হলে…”
মনোবীণার আর সহ্য হল না, খপ করে স্বামীর হাত ধরে টানতে টানতে বিছানায়। “কী হয়েছে তোমার বুকে?”
“ব্যথা?”
“কই আগে তো বলোনি?”
“বলে তোমাকে—মানে তোমাদের অনর্থক উ-উদ্বেগ— উদ্বিগ্ন করব—তাই বলিনি।”
“উদ্বিগ্ন! ন্যাকামি! কবে থেকে হচ্ছে ব্যথা?”
“তা হচ্ছে—” ফণীশ্বর মাথা হেলালেন সামান্য, “হচ্ছে আজকাল। মাঝে মাঝে। সরোজ সেই পা-ভাঙার সময় থেকেই দেখছে। ভয়ের কিছু নেই! এই বয়েসে হয় একটু। কলকবজার ব্যাপার তো! পুরনো হয়ে গেলে আলগা হয়ে পড়ে।”
“আচ্ছা!… তা মনসা তোমায় দেখল!”
“সঙ্গে সঙ্গে।”
“এত খাতির!”
“বলো কী! গায়ে-গায়ে থাকি। পা-ভাঙার সময় থেকেই তো দেখছে আমাকে। …তা তুমি কিন্তু ওই যে মা মনসা মা মনসা করো—ওটা কিন্তু ঠিক নয়। সরোজ ভাল ডাক্তার। হরেনবাবুর মাকে যমের হাত থেকে ফিরিয়ে আনল, দত্তর তো…”
মনোবীণা ধমক মেরে কথা থামিয়ে দিলেন স্বামীর। “যাও যাও ডাক্তার দেখিয়ো না। অমন ডাক্তারকে আমি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিই। …তা ছাড়া মনসাকে মনসা বলব—তাতে তোমার অত গায়ে লাগার কী আছে! আমি বলব, একশো বার বলব আমার খুশি!
“বললে তো কারুর মুখে হাত চাপা দেওয়া যাবে না।”
“দেবার চেষ্টা করে দেখো, হাত মুচড়ে দেব!”
“ভাঙা হাত, না, আস্ত হাত।”
“আস্ত হাত।”
“সর্বনাশ! তা তুমি এত খেপে গেল কেন?”
“তুমি খেপাবে, আমি খেপব না। ..কী বলল মনসা তোমার বুক দেখে?”
“বলল, মাঝে মাঝেই দেখিয়ে নিতে।”
“মাঝে মাঝে দেখাতে বলল, রোজ নয়?”
“কই তেমন কিছু তো বলেনি।”
“পান খেয়েছ কোথায়?”
“পান! দোকানে! কেন?”
“মুখ দেখে মনে হচ্ছে, মনসা তোমায় চা পান খাইয়ে আতিথ্য করেছে!”
“পা-ন! না, পা-ন তেমন কই?”
“কাল থেকে বাড়ির বাইরে যখন যাবে—খেঁদা তোমার সঙ্গে থাকবে। আমার হুকুম
চার
বর্ষা ঘোরতর হয়ে উঠল। ভাদ্র মাস। ফণীশ্বর একটু বেশি রকম মনমরা। বৃষ্টিবাদলা হলেই সকাল থেকে নেতিয়ে থাকতেন, দুপুরে বড় বড় শ্বাস ফেলতেন ; আর বিকেল হলেই খেঁদাকে ডাকতেন। ‘ওরে খেঁদু, নে। একবার চেটোর বাড়ি যাব।”
খেঁদার বাবা ছিল ফণীশ্বরের অফিসের খাস পিয়ন। চাকরি থেকে যখন ছুটি পেলেন ফণীশ্বর, খেঁদার বাবা তার ছেলেটিকে সাহেবের হাতে গুঁজে দিল। পাঁচ পাঁচটা ছেলে খেঁদার বাবার, খেঁদা ছোট। ধরে করেও তো পাঁচ ছেলের কাজ জোটানো সম্ভব নয়। কাজেই খেঁদা হল ফণীশ্বরের ফাউ। তা ছেলেটাকে নিজের কাছে রেখে রেখে মানুষ করেছেন ফণীশ্বর। সামান্য লেখাপড়া শিখিয়েছেন। বয়েসটা বেটার যোলোও হয়নি তায় রোগা-পাতলা, বেশ ট্যারা। ফণীশ্বরের ইচ্ছে—এবার ধরে-করে কোথাও ঢুকিয়ে দেবেন কাজে। থাকবে এখানেই। খোকার কারখানায় ঢোকাতে পারলে অবশ্য এখানে থাকা হবে না।
খেঁদা তার প্রতিপালকের পরম ভক্ত। প্রতিপালিকারও। আবার প্রতিপালিকাকে ভয়ও পায় ভীষণ। মনোবীণা তাকে এ-বেলায় যদি মাথায় তোলেন, ও-বেলায় গালমন্দ করে ভূত ভাগিয়ে দেন।
খেঁদার সবই ভাল। দোষের মধ্যে সে হিন্দি সিনেমার নামে পাগল, আর বিড়ি টানে লুকিয়ে লুকিয়ে।
মনোবীণার হুকুম, খেঁদা ছাড়া কর্তার বিকেলে বেরুনো চলবে না। তা গিন্নির হুকুম মেনেই তিনি খেঁদাকে নিয়ে বেরোন।
খেঁদা বড়বাবুর সঙ্গে বেরিয়ে যায়, ফেরে বাবুর সঙ্গেই সন্ধে উতরে, কোনও দিন সামান্য রাত করে।
বাড়িতে কাজকর্মের অসুবিধে যে না-হয়, এমন নয়, তবু মনোবীণা তাঁর হুকুম পালটাননি।
একদিন মনোবীণা স্বামীকে বললেন, “তুমি ওকে চোখে চোখে রাখো, না ছেড়ে দাও?”
ফণীশ্বর বললেন, “সে কি কথা! ওই তো আমায় চোখে চোখে রাখবে বলে পেছনে জুড়ে দিয়েছ। গোয়েন্দাগিরি! ওকেই তুমি জিজ্ঞেস করো।”
মনোবীণা বললেন, “গোয়েন্দা লাগাব কেন? হার্টের রোগী তুমি, পথে-ঘাটে যদি একটা বিপদ হয় ; সাবধান হবার জন্যেই সঙ্গে নিয়ে যেতে বলি।”
ফণীশ্বর বললেন, “তা হলে আর কথা কেন! ও থাকে।”
“কোথায় থাকে?”
“চেটোর বাড়িতে বন্ধুদের আসরে তো ওকে পাশে বসিয়ে রাখতে পারি না ; বাইরে কোথাও থাকে। ওকে জিজ্ঞেস করো।”
“অন্য সময়—? যখন ইয়ারদের আড্ডায় থাকো না—তখন ও কী করে?”
“আমাকে ফলো করে।”
“ও!… তো তোমার ছেলে বলছিল, বাবার হার্ট নিয়ে ছেলেখেলা কোরো না, মা! হার্টের অসুখের মজা হল, আজ এখন এই—তো তখন একেবারে ওই।”
“ঠিকই বলেছে। কারেক্ট। হার্ট এই—ঠিক এই মুহূর্তে হয়তো ছক্কার দান ফেলেছে, পরের মুহূর্তে অক্কার দান ফেলবে।”
“আমায় ভয় দেখাচ্ছ!”
“তোমায় ভয় দেখাব! তুমি হলে ভয়তারিণী ভয়ভঞ্জনা…!”
“দেখো, ঠুসে ঠুসে কথা বলবে না। এক্কেবারে বলবে না।.. যখনই বলো, বুকটা কেমন কেমন করছে—সঙ্গে সঙ্গে তোমার হুকুম মতন ওই মা মনসাকে ডাকতে হয়। আমার তো গা জ্বালা করে, মাথা আগুন হয়ে ওঠে ওকে দেখলে। তবু তোমার বায়না শুনে ডাকতে হয়।… হাজার বার করে বলছি, মনসা কিচ্ছু জানে না, মাদি মদ্দা হলেই কি সব জেনে বসে থাকবে। আমাদের জয়রাম ডাক্তার কত বড়, তাকে দেখাও, তা তুমি দেখাবে না কিছুতেই।”
ফণীশ্বর বললেন, “জয়রাম খোস পাঁচড়ার ডাক্তার। সে হার্টের কী বুঝবে?”
“অত বড় ডাক্তার…?”
“দুঃ ।”
“বেশ, তবে চৌধুরি ডাক্তারকে দেখাও।”
“সেটা তো ডাক্তার নয়, টাকার কল। টাকা টাকা করে বেটার এমন হয়েছে, শুনেছি, নিজের শাশুড়িকে দেখতে গিয়ে ফিজের জন্যে হাত বাড়িয়ে ফেলেছিল। ওকে জেলে দেওয়া উচিত।”
“শহরে আর ডাক্তার নেই?”
“রায় ভাল ডাক্তার। রায়কে দেখিয়েছি। বলেছে, দাদা মিস সরোজিনী গুপ্ত এ-ব্যাপারে ভাল বোঝেন। আপনার চয়েস ঠিক হয়েছে। তা ছাড়া বাড়ির পাশেই থাকেন উনি, ইমারজেন্সিতে উনি যত হেলপফুল হবেন—আমরা অতটা হব না।”
মনোবীণা বিরক্ত হয়ে বললেন, “যত্ত ছুতো! আচ্ছা, আমি দেখছি।”
ফণীশ্বর কিছু বললেন না। মনে মনে হাসলেন।
সপ্তাহ খানেক পরের কথা। মনোবীণা গিয়েছিলেন, পাল মশাইয়ের বাড়ি, সন্ধেবেলায়। পালগিন্নি বারবার বলে পাঠাচ্ছিলেন। তিনি নিজে সদ্য ভুগে উঠেছেন, শরীর বড় দুর্বল। পালগিন্নির বড় ইচ্ছে, এবারে বাড়িতে দুর্গাপুজো করেন প্রতিমা গড়িয়ে। সংসারে অনেক শুভ ঘটনা ঘটেছে, সবই মায়ের কৃপায়। এবার মাকে যদি এনে না বসান তা হলে কী চলে! এ-ব্যাপারে দিদির পরামর্শ দরকার। মনোবীণা হলেন পাড়ার সবচেয়ে যোগ্য পরামর্শদাতা।
পালবাড়ি থেকে ফিরছিলেন মনোবীণা। ঝিরঝির বৃষ্টি পড়ছে। পালবাড়ির খাস-ঝি রাধা ছাতা আর টর্চ নিয়ে মনোবীণাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছিল। গলিতে আলো কম। সামান্য কাদা জমেছে।
মনোবীণা ধীরে ধীরেই আসছিলেন। পা টিপে টিপে, সাবধানে। গড়াইদের বাড়ি পেরিয়েছেন, হরেনের ছোট্ট চা-খাবারের দোকান পাশে, গায়ে এক লম্বাটে রক, হঠাৎ রাধা টর্চের আলো ফেলে বলল, “ওমা, খেঁদা।”
মনোবীণা তাকালেন। প্রায় অন্ধকারে বৃষ্টি বাঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছে খেঁদা।।
“তুই এখানে?”
খেঁদা যেন ধরা পড়ে গেছে। মুখে কথা নেই। চোর যেমন করে হকচকিয়ে যায় ধরা পড়ার পর সেইভাবে হকচকিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।
“এখানে তুই কী করছিস?”
খেঁদার মুখে কথা নেই।
“বাবু কোথায়?”
খেঁদা চুপ। বাবুর সঙ্গেই সে বেরিয়েছিল। বাবুর সঙ্গেই ফেরার কথা।
“কথা বলছিস না?” মনোবীণা ধমকে উঠলেন।
খেঁদা ভয় পেয়ে বলল, “বড়বাবুকেই খুঁজছি।”
মনোবীণা বলতে যাচ্ছিলেন, বাবু কি গোরু ছাগল না কচি খোকা যে তুই তাকে খুঁজতে বেরিয়েছিস রাত্তির বেলায়! কথাটা মুখ ফসকে বেরুতে দিলেন না, জিবের ডগায় আটকে নিলেন। বললেন, “কেন, বাবু তোর সঙ্গে ছিলেন না?”
খেঁদা মাথা নাড়ল। “ছিলেন, না ছিলেন না। …বড়বাবু…!”
মনোবীণার কী মনে হল, মুখ তুলে তাকালেন। বিশ তিরিশ পা দূরে মা মনসার বাড়ি। সদর বন্ধ।
মনোবীণা খেঁদাকে বললেন, “আয় তুই।”
খেঁদা মুখমাথা নিচু করে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে মায়ের পিছু ধরল, ঠিক যেন চোর-আসামী ধরা পড়ে পুলিশের পাশে পাশে চলেছে।
বাড়ি এসে মনোবীণা খেঁদাকে সার্চ করলেন। প্যান্ট, জামা, ট্যাঁক—কিছুই বাদ দিলেন না।
খেঁদার কাছ থেকে অনেক কিছু পাওয়া গেল। সিনেমার টিকিটের ভেঁড়া কাগজ, নতুন পুরনো, সরু চিরুনি, একটা পেট্রল লাইটার, বিড়ি আর দুটো দুমড়ানো সিগারেট, সিনেমার একটা চটি বই, নগদ সাড়ে পাঁচ টাকা, আধ-প্যাকেট চানাচুর, একটা লোহার আংটি ইত্যাদি।
মনোবীণা বললেন, “এসব থাক এখানে। তুই নীচে যা। …আজ তোর খাওয়া বন্ধ। কাল তুই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবি। এখানে তোর জায়গা হবে না। চোর, বদমাশ, মিথ্যুক, শয়তান। ডুবে ডুবে জল খাওয়া দেখাচ্ছি তোকে।”
খেঁদা প্রায় কেঁদে ফেলেছিল, “মা আমার দোষ নেই। বড়বাবু—”
“চোপ। হারামজাদা। দেখাচ্ছি তোকে। যা আমার চোখের সামনে থেকে। বেরিয়ে যা।”
খেঁদা মুখ নিচু করে বেরিয়ে গেল। মনোবীণা বিছানায় বসে পড়ে হাঁপাতে লাগলেন।
পাঁচ
ফণীশ্বর বাড়ি ফেরার পর পরই মনোবীণার ঝাঁপিয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তিনি ঝাঁপালেন না। এমনকি, এতটা দেরি কেন, খেঁদা কেন অমুক জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল—সেসব কথাও তুললেন না। ফণীশ্বরের চোরের মন—নিজেই দু‘একবার খেঁদা, বৃষ্টি, চেটো, ঘাড়ের ব্যথা—ইত্যাদি প্রসঙ্গ তুলতে গিয়ে দেখলেন, গিন্নি হয় কথাগুলো কানেই তুলছেন না, না-হয় ঘরের বাইরে চলে যাচ্ছেন। বাক্যালাপের সুযোগই হচ্ছে না।
মনোবীণা কিন্তু স্বামীকে যে নজর করছিলেন না—তাও নয়। আড়ে আড়ে করছিলেন। স্বামীর চোখ মুখ তাঁর তো কম জানা নয়। ওই চোখের মধ্যে যে পাতলা ঢুলুঢুলু ভাব ছিল তাও তিনি নজর করেছেন। লক্ষ করেছেন, কথা বলার সময় ভদ্রলোকের দু’চারটে কথা এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল, শব্দ পিছলে যাচ্ছিল জিবের ডগা থেকে।
ফণীশ্বর পাকা লোক। তিনি বুঝতে পারছিলেন, বাঘ বা বাঘিনী এখন আশপাশে নিজেকে আড়াল করে রেখে শিকারটিকে দেখছে। যথাসময়ে লাফ মারবে।
ফণীশ্বর অনুমান করার চেষ্টা করতে লাগলেন, কখন কোন দিক থেকে কী ধরনের আক্রমণ ঘটলে তিনি বাঘিনীকে জব্দ করতে পারবেন।
খাওয়া সেরে ফণীশ্বর শুয়ে পড়লেন।
মনোবীণা খানিকটা পরে ঘরে এলেন।
ফণীশ্বর ভাব করলেন যেন ঘুমিয়ে পড়েছেন। মনোবীণা নিত্যকার মতন ঘরের মধ্যে ঘুরলেন ফিরলেন, ছোটখাটো কাজ সারলেন। দরজা বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন। কোনও কথাই বললেন না।
ফণীশ্বর অনুমান করেছিলেন, নিভৃতে শয্যায় তাঁর ওপর আক্রমণটা ঘটতে পারে। তিনি মনে মনে নিজেকে তৈরি করে রেখেছিলেন। হায় রে, কিছুই যে ঘটছে না।’
রাত বাড়তে বাড়তে বুঝি মাঝরাত পেরিয়ে যাচ্ছিল, ফণীশ্বর বাস্তবিকই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, হঠাৎ পেটের কাছে খোঁচা খেয়ে ঘুম জড়ানো গলায় বললেন, “আঃ!”
আবার খোঁচা। বার দুই তিন।
ঘুম ভাঙল ফণীশ্বরের। কী হল?”
“আমার বুকটা কেমন করছে। উঠতে পারছি না। জল দাও!”
ফণীশ্বরকে উঠতে হল। “অম্বলের ব্যথা?”
“উঃ! মাগো—”
“কী খেয়েছিলে রাত্তিরে?” বলতে বলতে ফণীশ্বর উঠে পড়ে ঘরের বাতি জ্বাললেন। জল গড়িয়ে দিলেন স্ত্রীকে।
মনোবীণা উঠে বসলেন। বিছানায় পা ছড়িয়ে বসে আছেন।
“নাও। …ইয়ে একটু জোয়ানের আরক খাবে নাকি? বুকের তলায় ব্যথা তো! অম্বল! গ্যাস আটকে গেছে। “
জলের গ্লাসটা নিলেন মনোবীণা, তারপর আচমকা, একেবারে আচমকাই বললেন, “মনসা তোমায় যে ওষুধটা খেতে দেয়—সেটা দাও!”
ফণীশ্বর থতমত খেয়ে গেলেন।
“মনসা—মানে সরোজের ওষুধ?”
“হ্যাঁ।”
“সেটা তো হার্টের…।”
“আমারও হার্ট।”
ফণীশ্বর বললেন, “কে বলল! তোমার অম্বল। গ্যাসট্রিক। গ্যাস—।”
“হার্ট। আমার শরীর আমি ভাল বুঝব না, তুমি বুঝবে?”
“তুমিই বোঝে। কিন্তু কথা নেই, বার্তা নেই, হুট করে হার্টের ওষুধ খেয়ে বসবে।”
“খাব।”
“তারপর যদি কিছু হয়!”
“হলে পাপ চুকবে।…দাও ওষুধটা দাও।”
ফণীশ্বর বড় বিপদে পড়লেন। হার্টের ওষুধ তাঁর কাছে কিছু নেই। সরোজ তাঁকে কোনও ওষুধ দেয়নি খেতে। কেননা, এই বয়েসেও হার্টের এমন কোনো গণ্ডগোল নেই যে নিত্য কোনও ওষুধ খেতে হবে। ওষুধের ব্যাপারে সরোজ বড় কড়া। হুটহাট ওষুধ খাওয়া সে পছন্দ করে না। একটা ভিটামিন ট্যাবলেট খেতে চান খাবেন। পেটে বুকে চাপ বুঝলে—সোডামিন্ট। আপনার তো সোডার অভ্যেস ভালই আছে। কোনও ক্ষতি হবে না।’…ফণীশ্বরের কাছে সেই সোডামিন্ট ট্যাবলেট পড়ে ছিল। মাঝে মাঝে স্ত্রীকে দেখিয়ে সেটাই খেতেন। কিন্তু আজ এই সময়—!
ফণীশ্বর তবু ওষুধ খোঁজার ছুতো করে একটা কী এনে দিলেন।
মনোবীণা দেখলেন ওষুধটা। বললেন, “এটা তো তোমার ত্রিফলার কবিরাজি বড়ি।”।
“আরে না না।”
“না না মানে! আমি জানি না। গুণ্ডু কম্পানির ত্রিফলা বড়ি। নিজের হাতে উষ্ণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে আমি তোমাকে খেতে দিই।”
ফণীশ্বর বিপাকে পড়ে গেলেন। “ও! তা হলে ভুল হয়ে গেছে। ঘুম চোখে মাঝরাত্তিরে—দাও তবে?”
“তোমার আজকাল খুব ভুল হচ্ছে, না?” মনোবীণা এবার পা গুটোলেন।
“ভুল! কই না!”
“খুব হচ্ছে, রোজই হচ্ছে। উত্তরে যাব বললে দক্ষিণে যাও, চেটোর বাড়ি যাচ্ছি বলে মনসার বাড়ি যাও।”
ফণীশ্বর বুঝতে পারলেন, বাঘিনী সময় মতন ঝাঁপ দিয়েছেন। প্রবল বেগে মাথা নেড়ে বললেন, “সরোজের বাড়ি যাই! কী আশ্চর্য! কে বলল? কোথায় সরোজ! কোথায় আমি!”
“যাও না?”
ফণীশ্বর ভয় পেয়ে গেলেন কিনা কে জানে, বললেন, “দরকার না-পড়লে যাব কেন? এই হার্টের কোনও…”
“আজ যাওনি?”
ফণীশ্বর বললেন, “খেঁদা বলেছে?”
“খেঁদাকে তুমি উচ্ছন্নে পাঠিয়ে দিলে! ছিছি! ওই হারামজাদাকে তুমি টাকা খাইয়ে বশ করে নিয়েছ! ওকে পয়সা দাও সিনেমা দেখার, বিড়ি-সিগারেট ফোঁকার। ওকে বলো, যা খেঁদা পিকচার দেখে আয়। আর নিজে গিয়ে ওঠো মনসার বাড়ি। লজ্জা করে না তোমার! বুড়ো হাবড়া। এই বয়সে কোথায় ধম্ম কম্ম করবে, ঠাকুরুদেবতার কথা ভাববে, তা নয়—কোথাকার একটা মদ্দাটে মেয়েছেলের বাড়িতে গিয়ে বসে বসে ফস্টিনস্টি করো। ছি ছি! আমার মরতে ইচ্ছে করছে।”
ফণীশ্বর স্ত্রীকে দেখলেন। বললেন, “ফস্টিনস্টি করি না। ভগবানের দিব্যি। তোমার দিব্যি।.. মিথ্যে বলব না, সরোজের কাছে যাই। গল্প গুজব করি। আর ইয়ে একটু জিন খাই। ব্লু রিবন উইথ লাইম।”
“কী খাও?”
“জিন!…মেয়েরাই বেশি খায় ওটা। আমাদের কাছে কিস্যু নয়। জল। লেবু জল!”
“ওই মদ্দা মাগিটাও বুঝি খায় তোমার সঙ্গে?”
“এক আধ দিন। বেশির ভাগ দিন সরোজ সফট ড্রিঙ্ক খায়….”
“আর তুমি মদ গেলো!”
“ধুত, ও আবার মদ নাকি? আমাদের পেটে বার্লি…সেরেফ বার্লি….।”
স্বামীকে দেখতে দেখতে মনোবীণা বললেন, “তোমার যত দোষই থাক—এই মনসা-দোষ তো ছিল না। কী কুক্ষণে তোমার পা ভাঙল, আমি ছিলাম না বাড়িতে, আর ওই মনসামাগি এসে জুটল! আমার কী কপাল! কোথায় আমি কোন পাহাড়ে গিয়ে মায়ের পায়ে মাথা ঠুকে তোমার জন্যে মাদুলি নিয়ে এলাম মদের নেশা ছাড়াব বলে, তা ওটা যদি বা কমল একটু এটা একেবারে চড়চড়িয়ে বেড়ে গেল।”
ফণীশ্বরের মাথায় যেন বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে গেল। বললেন, “মাই গড। ঠিক তো! মাদুলি পরার পর থেকেই চেটোর আচ্ছা কমেছে বটে—বেশ কমেছে। কিন্তু ওই সরোজ আমায় চোঁ চোঁ করে টানছে। যেন ম্যাগনেট। দারুণ পাওয়ারফুল ম্যাগনেট। সত্যি তো— আগে কথাটা খেয়াল করিনি।”
মনোবীণা বিছানা থেকে নেমে পড়লেন। জলের গ্লাসটা এগিয়ে দিলেন স্বামীকে। ফণীশ্বর গ্লাস ধরলেন।
মনোবীণা কোনও কথা বললেন না। স্বামীর হাতে বাঁধা মাদুলির সুতোটা টেনে পট করে ছিড়ে ফেললেন। যথেষ্ট জোর আছে হাতে। মাদুলিটা ছুড়ে দিলেন জানলা দিয়ে। বললেন, “নাও, এবার তুমি তোমার ইয়ার বন্ধু চেটোর বাগানে চরে বেড়াও। ও বরং আমার সইবে। এতকাল সহ করেছি, আর না হয় ক’বছর—যতদিন না মরছি। কিন্তু ওই মনসা আমার সইবে না।”
ফণীশ্বর চতুরের মতন হাসলেন। বললেন, “মাদুলিটা তুমি ফেলে দিলে? তা ভালই করেছ! ওটা বোধ হয় ভুল মাদুলি ছিল। ‘ম’য়ের ভুল। এক করতে আরেক করছিল। তবে মনো, আমি আগের মতন চরে বেড়াব ঠিকই—কিন্তু সরোজকে তুমি গালমন্দ কোরো না। সত্যি সে ভাল। আমায় দাদা বলে। “
“বলুক। দাদা বললেই সাত খুন মাপ!”
“না ইয়ে—! মানে এর মধ্যে সরোজেরও একটা পার্ট ছিল। সে সবই শুনত, আর হাসত। বলত, দাদা—আপনি কিন্তু বউদিকে অনর্থক খেপাচ্ছেন। এটা চোর-পুলিশ খেলা হচ্ছে। বুড়ো বয়েসে এত মজার খেলাও খেলতে পারেন! ধন্যি আপনারা।”
মনোবীণা স্বামীর হাত থেকে খপ করে জলের গ্লাস কেড়ে নিয়ে ফণীশ্বরের মাথায় ঢেলে দিলেন।
বউ নিয়ে খেলা
শচীন আসতেই তার বন্ধুরা সাদর অভ্যর্থনা করে বলল, “আয় আয়, তোর পথ চেয়ে বসে আছি।”
শচীনের বন্ধু বলতে আপাতত এই ঘরে চারজন: প্রতাপ, সুবিমল, আশু আর হালদার। চারজনেরই বয়েস চল্লিশের কাছাকাছি। প্রতাপ হয়তো চল্লিশে পা দিয়েছে, বাকিরা সামান্য তফাতে দাঁড়িয়ে। প্রতাপের চেহারাও কলকাতার পুরনো বাবু-বাড়ির বংশধরদের মতন: গোলগাল, ফরসা, মাথায় টাক, চোখে চশমা। হগ মার্কেটে ফুলের দোকান প্রতাপের। আর তার বাড়ির বৈঠকখানায় বন্ধুদের আড্ডা। সুবিমল কলেজের বাংলা টিচার, আগে বোধ হয় কবিতা লিখত, এখন রচনাবই লেখে, কবিতার ভাঙা লাইন আর রচনা-বইয়ের স্থূলতার মতন তার চেহারা। চোখ মুখ ভাঙা ভাঙা দেখালেও গায়ে গতরে চর্বি জমেছে। আশু হল ইনকাম ট্যাক্সের উকিল। ছিপছিপে চেহারা, চোখে মুখে ঝরঝরে হাসি। গালের আধখানা জুলফি দিয়ে ঢেকে রেখেছে। হালদারই সবচেয়ে নিরীহ ধরনের; দেখলেই বোঝা যায় অম্লশূলের রোগী।
প্রতাপ তার চুরুটের পিছনে কাঠি করতে করতে বলল, “গিয়েছিলি?”
শচীন একপাশে বসল। বসে তার বাঁ হাতটা সুবিমলের দিকে বাড়িয়ে দিল। “পালস্টা একবার দেখ তো, ভাই?”
সুবিমল বলল, “কেন? জ্বর হয়েছে তোর?”
মাথা নাড়ল শচীন। “হার্ট সিঙ্ক করে যাচ্ছে। বাব্বা কী জিনিস দেখলাম। জঙ্গলের বাঘ দেখেছি। এ ভাই বাঘের বাবা। সরি, মা।”
আশু বলল, “খুলে বলো! আমরা হাঁ করে বসে আছি তোমার জন্যে। গজেন কাটলেট আনতে গিয়েছে। এসে পড়বে এখুনি।”
হালদার বলল, “কলকাতায় বড় কলেরা হচ্ছে। কাটলেটটা না খেলেই পারতেন।”
“রাখুন তো মশাই, কলেরা টাইফয়েড করেই আপনি গেলেন।”
প্রতাপ বলল, “ব্যাপারটা বল, শচীন।”
শচীন বলল, “ভাই আমি যথারীতি যথাস্থানে গিয়েছিলাম। একেবারে কাঁটায় কাঁটায় ছ’টা। পাঁচতলা বাড়ি, তেতলায় অফিস। লিফট নেই। উঠলাম ওপরে। অফিসের বাইরে দরজার সামনে টুলে এক দরোয়ানি মেয়ে বসে ছিল। হাতে কাগজ পেনসিল। নাম লিখে দিলাম। তারপর ডাক পড়ল।”
সুবিমল হাত বাড়িয়ে আশুর সিগারেটের প্যাকেট টেনে নিল।
শচীন বলল, “ঘরের মধ্যে ঘর। প্রথম ঘরে জনা চারেক মহিলা। লম্বা, বেঁটে, কালো ফরসা নানা টাইপের। চেহারায় সব ক’জনই পুষ্ট। আন্ডার সিক্সটি কেউ নয়।”
“বয়েস?”
“না না, বয়েস কেন হবে, কেজি-তে। মহিলারা কফি-ব্রেক করছিলেন, উইথ চানাচুর। ঘরে দিব্যি সেন্টের গন্ধ। আমায় দেখে চোখে চোখে খেলা চলল। গলায় ব্লটিং-চাপা হাসি।”
এমন সময় গজেন এল। লম্বা চওড়া চেহারা, মাথায় চুল কোঁকড়ানো, পরনে পাজামা পাঞ্জাবি। হাতে কাগজের ঠোঙায় কাটলেট।
প্রতাপ বলল, “ডিস্টার্ব করবি না, বোস। যা কাটলেটগুলো তোর বউদিকে দিয়ে আয় ভেতরে। চায়ের সঙ্গে দিতে বলবি।”
গজেন ভেতরে গেল। হাঁক মারল। আবার ফিরে এল।
শচীন বলল, “ঘরের মধ্যে আর একটা ছোট ঘরে ঢুকে দেখলাম, দারুণ ব্যাপার। মেঝেতে জুট কার্পেট, একপাশে ছোট সোফা, সামনে সেক্রেটারিয়েট টেবিল, ওপাশে বিশাল চেয়ার, এপাশে একটি মাত্র চেয়ার, ঘরের একদিকে এক ছোট আলমারি, গোটা দুয়েক ছবি ঝুলছে।”
“তুই বড় বেশি গৌরচন্দ্রিকা করছিস,” সুবিমল বলল।
শচীন বলল, “গাছে না উঠে এক কাঁদি তো হয় না, ভাই। ব্যাপারটা চোখে না দেখলে বুঝবে না, তবু মুখে বললাম।… তা টেবিলের ওপাশে ছিলেন রেহান লাহিড়ি।”
“রেহান! পুরুষ মানুষ নাকি?” আশু জিজ্ঞেস করল।
“না, মহিলা। লেডি। তবে পুরুষের কান কাটেন। একেবারে বয়কাট চুল, চোখের চশমা কালো কর্ড দিয়ে বুকের কাছে ঝুলিয়ে রাখেন, মাঝে মাঝে পরেন চোখে, আবার ঝুলিয়ে দেন বুকের ওপর। চেইন স্মোকার। রোস্টেড টোবাকো বোধ হয়, যা গন্ধ!”
হালদার বলল, “পরনে কি প্যান্ট?”
“না প্যান্ট নয়। অন্তত আজ প্যান্ট দেখলাম না। শাড়িই পরেছেন। তবে শাড়িটা নেহাত গায়ে জড়ানো। থাকে থাকে খুলে যায়।”
“ব্লাউজ-টাউজ ছিল না—?” আশু চোখ টিপে বলল।
“যেটুকু থাকার ছিল। মিনিমাম।… মুখে নো রংচং; হাতে ডবকা সাইজের ঘড়ি। গলায় এক পাথরের মালা।”
“তা ওজন-টোজন কেমন?” প্রতাপ জিজ্ঞেস করল।
“মিনিমাম পঁচাত্তর। আশি কেজিও হতে পারে।”
“বাপস! হাতি নাকি?”
“আজ্ঞে না। উনি আদিতে ছিলেন রোহিনী। রোহিনী থেকে রেহান।”
সুবিমল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল! “হায় বঙ্কিম!”
আশু বলল, “যাক, তারপর কী হল—শুনি!”
শচীন এবার একটা সিগারেট ধরাল। কয়েকটা টান মেরে বলল, “কথাবার্তা হল। তা প্রায় আধঘণ্টা মতন। আমায় কফি খাওয়ালেন।”
গজেন বলল, “কী কথাবার্তা হল সেটা বল! ওটাই তো আসল।”
শচীন বলল, “আমি স্পষ্টই বললাম, একটা ডিভোর্স কেস প্রায় সেটল্ড—সেটা আনসেটেল করতে হবে। শুনে রেহান তো প্রথমে চটে গেলেন। বললেন, দেখুন, আমরা মেয়েদের ইনটারেস্ট দেখার জন্যে এই অরগানিজেশান খুলেছি। আমাদের উদ্দেশ্য মেয়েদের স্বার্থ দেখা। আপনি ভুল জায়গায় এসেছেন।… আমাকে প্রায় উঠিয়েই দিচ্ছিলেন, কিন্তু অত সহজে কি আমাকে ওঠানো যায়! লাইফ ইনসিওরেন্সের এজেন্সি দিয়ে লাইফ শুরু করেছিলাম ভাই। ‘না’ কে ‘হ্যাঁ’ করাতে পারি। মিষ্টি কথা, ন্যাকা কথা, তৈল দান—শেষে পকেট থেকে চেক বই বার করে এক শো একান্ন টাকার অ্যাডমিশান চার্জ দিতেই রেহান আমায় তাঁদের ক্লায়েন্ট করে নিলেন। খাতায় নাম-ধাম লেখা হল। আমার নম্বর হল…” বলে শচীন পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করল—ব্যাগ হাতড়ে একটা রসিদ। বলল, “নম্বর হল, জিরো জিরো থার্টি ওয়ান।”
প্রতাপ হাত বাড়াল। “দেখি রসিদটা…।”
শচীন রসিদটা দিল।
দেখল প্রতাপ। বলল, “নামটা পশু ক্লেশ নিবারণ সমিতির মতন মনে হচ্ছে যে!”
“হ্যাঁ,” মাথা নাড়ল শচীন, “রেহানদের সমিতিও অনেকটা ওই ক্লাসের। ওটা মহিলা পীড়ন নিবারণ সমিতি গোছের।”
আশু বলল, “তা, ওখানে আর যে সব জিনিস দেখলে, যাঁরা কফি খাচ্ছিলেন—তাঁদের কেমন মনে হল, ক্লেশ আছে।”
শচীন বলল, “ভেতরে থাকতে পারে, ওপরে দেখলাম না। সকলেই বেশ ব্রে-শ-”।
আশু জোরে হেসে উঠল। সুবিমল বলল, “তোর নজর ভাল।”
এমন সময় ভেতর থেকে চা এল। চা আর কাটলেট।
গজেন সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল।
হালদার বলল, “ব্যাপারটা একটু ইয়ে হয়ে যাচ্ছে না?”
কাটলেট চিবোতে চিবোতে আশু বলল, “ইয়ে হবে কেন! যা হওয়া উচিত তাই হচ্ছে।”
হালদার সাহস করে কাটলেটের দিকে হাত বাড়াতে পারছিল না। গন্ধটা নাকে লাগছিল! প্রতাপ কচকচ করে স্যালাড চিবোচ্ছে। জিভে জল আসছিল হালদারের।
“না, আমি বলছিলাম”, হালদার ঠোঁট চাটল, “ব্যাপারটা তো তেমন সিরিয়াস নয়। শচীনবাবুর স্ত্রী সত্যি সত্যি তো আর ডিভোর্স করছেন না।”
“কে বলল?” শচীন আবার খানিকটা কাটলেট মুখে পুরল। “আর কত সিরিয়াস হবে! আমার বউ আজ তিন হপ্তা হল তার বাপের বাড়ি চলে গেছে। ও-বাড়িতে গেলে দেখা করে না। ফোন করলে ধরে না। চিঠি লেখেছি, জবাব দেয়নি। বলছিল, লিগ্যাল হেল্প নিচ্ছে। নিতেই পারে। ওর এক কেমন মাসতুতো দাদা ছিল। আই থিঙ্ক হার লাভার, প্রি-ম্যারেজ। সে বেটা উকিল। এই চান্সে বেটা বগল বাজাবে।”
প্রতাপ বলল, “না না, কাজটা ভালই হয়েছে। বরং আমি বলব, স্টেটসম্যানে বিজ্ঞাপনটা বেরিয়ে শচীনকে খুব হেল্প করল। না কি সুবিমল?”
সুবিমল চায়ের কাপ টানল। “নিশ্চয়। একেই বলে গডস ব্লেসিং।”
“বিজ্ঞাপনটা ভাগ্যিস আশুর চোখে পড়েছিল।”
আশু বলল, “আমার চোখে সবই পড়ে। শচীনদার যা হাল দেখেছিলাম…”
হালদার হাত বাড়িয়ে কাটলেটের সিকি ভাগ তুলে নিল। “না, আমি বলছিলাম—এ-সব ব্যাপার যদি নিজেরা সেটল করা যেত!”
“কেমন করে যাবে?” শচীন বলল, “আমার বউয়ের দশ দফা দাবি। চার দফা আমি কোনো রকমে মেটাবার চেষ্টা করতে পারি।”
“কী কী?” প্রতাপ জিজ্ঞেস করল।
“ধর, যদি পাই—ধারকর্জ করে একটা ফ্ল্যাট কেনার টাকা যোগাড় করতে পারি। দুই: দু’বছর অন্তর বউকে হাওয়া খাওয়াতে নিয়ে যেতে পারি কলকাতার বাইরে। তিন: ঝি না থাকলে হোটেলে খেতে পারি। চার: আমি কিছু টাকা বউয়ের হাত-খরচা হিসেবে স্পেয়ার করতে পারি। ব্যাস,..আর কিছু পারব না।”
আশু বলল, “বাকি ছ’ দফার মধ্যে কোনটা একেবারেই পারবে না।”
“বাচ্চা! বাচ্চা আমদানি আমার হাতে নয়। আমার বউকে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না, তার কপালে যদি না থাকে আমি কী করব? এ তো কুমারটুলিতে অর্ডার দিলে পাওয়া যায় না।”
প্রতাপ বলল, “তোর অর্ডার প্লেস সঠিক জায়গায় কর, হয়ে যাবে।” বন্ধুরা হোহো করে হেসে উঠল।
ঘটনাটা যেভাবে ঘটেছিল একটু বলা দরকার।
শচীন হল সেই ধরনের মানুষ যার মধ্যে এক ধরনের পৌরুষ আছে। অর্থাৎ সে তেজি এবং তেড়া। ভয়ঙ্কর আড্ডাবাজ এবং অসংসারী। সে বউকে ঠিক ততখানি তোয়াক্কা করতে নারাজ যতটা করলে ঘরে শান্তি থাকে। এই স্বভাবের জন্যে তাকে বিয়ের পর থেকেই পস্তাতে হচ্ছে। আজ চার বছরে তার বউ—মলয়া বার ছয়েক শচীনকে জব্দ করার জন্যে নানা রকম কাণ্ড করেছে। একবার, বিয়ের নতুন নতুন অবস্থায় চার আউন্স ক্যাস্টর অয়েল খেয়েছিল। শচীন তাতে যত না জব্দ হয়েছিল তার চারগুণ হয়েছিল মলয়া নিজেই। ধাত ছেড়ে যাবার জো হয়েছিল তার। পরের বার মলয়া আর অয়েলে যায়নি, ট্যাক্সি ধরে চলে গিয়েছিল দক্ষিণেশ্বরের গঙ্গায়। ভেবেছিল হয় আত্মবিসর্জন দেবে, না হয় সন্ন্যাসিনী হবে। সারাদিন ভেবেও মতি স্থির করতে পারেনি। রাত্রে ফিরে এসে দেখে শচীন পাঞ্জাবির দোকানের কষা মাংস খাচ্ছে, তার পাশে ছোট এক বোতল হুইস্কি। মলয়াকে দেখে শচীন বলল, “আমি ভাবলাম তুমি দুর্গাপুরে লাটুদার কাছে বেড়াতে গেছ।” স্বামীর ব্যবহার দেখে ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠেছিল মলয়া। তৃতীয়বার মলয়া টানা বাহাত্তর ঘণ্টা উপবাস করেছিল পলিটিক্যাল চাল মেরে। শচীন তাতেও কাবু হল না, বরং শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে বলে এল, “আমি অফিসের কাজে নর্থ বেঙ্গল যাচ্ছি, আপনাদের মেয়েকে দেখবেন।” এইভাবে চতুর্থও পঞ্চম বারের পর মলয়া ইঁদুর মারা বিষ খেয়েছিল, কিন্তু ভেজাল বিষ তেমন কোন কাজ করল না শরীরে; মলয়া বার দুয়েক বমি করল। শচীন বলল, “চলো তোমায় গাইনির কাছে নিয়ে যাই। এই সময়ে বমি ভাল।”
মলয়া শেষ পর্যন্ত বুঝে ফেলেছিল, শচীন বদলাবার নয়। তার কাছে স্ত্রী আর ডাক্তারের কাছে স্টেথসকোপ একই জিনিস। দুটোই গলায় ঝোলাবার। কাজে লাগানোর যন্ত্র। শচীনের না আছে বউ নিয়ে আদিখ্যেতা, না গদগদ ভাব, না স্বার্থত্যাগ। দায়িত্বহীন, আড্ডাবাজ, নেশুড়ে, নিস্পৃহ—এই মানুষটাকে আর সহ্য করা সম্ভব হল না মলয়ার। তার ওপর বাচ্চাকাচ্চাও হল না বেচারির। কী নিয়ে থাকবে সে?
চটেমটে মলয়া বলল, “তোমার সঙ্গে আমি থাকব না।”
কাঁচি দিয়ে গোঁফ ছাঁটতে ছাঁটতে শচীন বলল, না থাকলে—!”
“এত বড় কথা! বেশ, আমি ডিভোর্স করব তোমায়।”
“করো ।”
“তোমায় আমি শায়েস্তা করব, তবে আমার নাম।”
“ভয় দেখিও না, আমি তোমার মতন একগণ্ডা মেয়েছেলে পকেটে পুরতে পারি।”
“পারো বলেই তো আমার এই হাল।… আমি আজই চলে যাচ্ছি।”
“যাও। আই ডোন্ট কেয়ার।”
“অল রাইট।”
মলয়া তার ট্রাংক সুটকেস গুছিয়ে, লকারের চাবি নিয়ে সোজা বাপের বাড়ি চলে গেল সেই দিনই। শচীন মাথা ঘামাল না। মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত। সাত দিনেই সব ঠিক হয়ে যাবে।
সাত দিনের হিসেব পনেরো, তারপর একুশ দিনে গিয়ে দাঁড়াল। মলয়া আর ফিরল না। শচীন প্রথম দিকে গ্রাহ্য করেনি। ধীরে ধীরে গ্রাহ্য করতে বাধ্য হল। বাড়িতে তার দ্বিতীয় আত্মীয়া নেই। ঠিকে ঝি আর ঠিকে বামুনের ভরসায় সংসার। তারা সকালটা চালিয়ে দেয়, বিকেলে কেউ আসে না। শচীন বাড়ি থাকে না, আসবে কেমন করে। সব দিকেই অসুবিধে হতে লাগল। বাধ্য হয়েই শচীন একদিন ফোন করল শ্বশুরবাড়িতে। মলয়াই ফোন ধরেছিল। বলল, “উকিলের সঙ্গে কথা হচ্ছে। কানুদা বলেছে, সব ব্যবস্থা করে দেবে। আজকাল ডিভোর্স পাওয়া জল-ভাত। তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।”
শচীন বলল, “বাঃ, নেই মানে? তুমি আমার লিগ্যাল ওয়াইফ। কানু দাদার বাড়ি পেয়েছে!”
“আমি তোমার ওয়াইফ নই। লিগ্যাল ঝি ছিলাম। আর থাকব না। তুমি ছোটলোক, শয়তান।”
শচীন বলল, “বাড়াবাড়ি কোরো না, পস্তাতে হবে।”
“তোমাকেও হবে।” ফোন ছেড়ে দিল মলয়া।
শচীন তার পৌরুষকে খাটো করে গেল শ্বশুরবাড়িতে। শ্বশুরমশাই বললেন, “তুমি যা করেছ এরপর কোন মুখে এবাড়িতে এসেছ! মালু যাবে না।”
শাশুড়ি কেঁদে বললেন, “মেয়ের তুমি যা হাল করেছ, ছিছি, তোমায় পুলিশে দেওয়া উচিত।”
বড় শালা বললে, “মালুকে তুমি শ্যাটার করে দিয়েছ। ওর নার্ভ ব্রেক করেছে। ওকে আমরা আর পাঠাব না। ডিভোর্স স্যুট ফাইল করব।”
শচীন ফিরে এল। বুঝল, মাথা-খাওয়া আদুরে মেয়ের মাথা আরও নষ্ট করে দিচ্ছে তার বাপের বাড়ির লোক। এমনিতেই মলয়া আদুরি, ন্যাকা, জেদি, ছিটেল, অপদার্থ। এখন তার আরও মাথা খাবার ব্যবস্থা হচ্ছে।
শচীনের দুঃখই হল। বউ তার, অথচ মাতব্বরি করছে বাইরের পাঁচজনে।
বন্ধুদের কাছে শচীন সবই বলত। বন্ধুরা শুনত, কোনো উপায় বাতলাতে পারত না। ‘ওয়েট অ্যান্ড সি’ করে চলত।
শেষ পর্যন্ত আশুই একদিন বিজ্ঞাপনটা আবিষ্কার করে ফেলল। একটা কুকুর বাচ্ছা কিনবে বলে আশু স্টেটসম্যান-এর বিজ্ঞাপন হাতড়াচ্ছিল, হঠাৎ চোখে পড়ল এক মজাদার বিজ্ঞাপন। আশুর মাথা বড় সাফ। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুদের কাছে চালান করে দিল কাগজটা।
বন্ধুরা প্রথমটায় সন্দেহ প্রকাশ করেছিল। আজকাল নারী জাগরণের দিন। চতুর্দিকে হইহই চলছে। লিব মুভমেন্ট, নারীবর্ষ। নানা ধরনের নারী সমিতি আসরে নামছে। তারা ভেবেছিল সেই রকম কিছু একটা হবে। এই সমিতি মেয়েদের নানান সমস্যা ও সামাজিক পীড়ন নিয়ে মাথা ঘামাবার জন্য তৈরি হয়েছে। তা হোক। কিন্তু ব্যাপারটা মেয়েদের, শচীনের মামলা তারা নেবে কেন?
আশু বলল, “কেন নেবে না! কেস শচীনদার একলার নয়, সঙ্গে বউদি আছে।”
সুবিমল বলল, “একবার ট্রাই নিতে পারে শচীন। নেয় নেবে, না নেয় না নেবে। ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে তো দেবে না।”
প্রতাপ বলল, “তুই চলে যা শচীন। কেঁদে ককিয়ে পড়বি। ট্রাই ইয়োর লাক।”
শচীন বন্ধুদের পরামর্শ কানে তুলে বলল, “বেশ যাব।”
দিনক্ষণ ঠিক করে দিল বন্ধুরা। শচীন যথারীতি গেল। ফিরে এসে যা বলল—তার বিবরণ আগেই দেওয়া হয়েছে।
দিন দুই বাদে অফিসে শচীন ফোন পেল। রেহানের গলা। বলল, “আপনাকে আজ একবার আসতে হবে।”
“অফিসে?”
“হ্যাঁ। পাঁচটার পর আসুন। বাই ফাইভ থারটি।”
ঢোঁক গিলে শচীন বলল, “অন্য পার্টিও কি থাকছে?”
“অন্য পার্টি? ও!… না কেউ থাকছে না। আমাদের কিছু কোশ্চেন আছে। ঘণ্টা খানেক সময় লাগবে। আপনার ফিজ লাগবে পঁচিশ টাকা।”
“পঁচিশ?”
“মেয়েদের কাছে পনেরো নিই। আপনার কাছে তিরিশ নেওয়া উচিত ছিল আমরা কনসিডার করেছি…। যদি আপত্তি থাকে আসবেন না।”
“না না আমি যাব।”
হগ মার্কেটে প্রতাপকে একটা ফোন করে খবরটা জানিয়ে দিল শচীন। “ওরে আমার ডাক এসেছে। পাঁচটায় যাচ্ছি। পঁচিশটা টাকা গচ্চা যাবে।”
প্রতাপ বলল, “সঙ্গে অ্যাসিস্ট্যান্ট নিবি? আমি খালি আছি।”
“না। একলা যাব। কবি বলেছেন—একলা চলো রে!”
“যা তবে। সন্ধেবেলায় বাড়িতে আসিস। শুনব।”
শচীন যথাসময়ে ওয়েলেসলিতে হাজির হল।
আগের মতনই সব। সেই আয়া, স্লিপ লেখা। ডাক এল সঙ্গে সঙ্গেই।
রেহানের ঘরে ঢোকার আগে শচীন আজ মাত্র দুজন মহিলাকে দেখল। একজন টাইপ করছে। অন্য জন ফাইল ঘাঁটছিল।
রেহানের ঘরে ঢুকতেই রেহান বলল, “আসুন।”
শচীন নমস্কার করল। “দেরি হয়ে গেল?”
“না, বসুন।”
বসল শচীন। দেখল রেহানকে। রেহানের পরনে তাঁতের সাদা শাড়ি, কালো পাড়। গায়ের জামা সাদা। আজ গলায় মালা নেই, যথারীতি গলায় চশমা ঝুলছে। রেহান একটা ফাইল টানল। পাতা ওলটাল। “আপনার ফাইল দেখলাম। কিছু ডিটেল দরকার।”
“বলুন?”
“আপনার স্ত্রীর ঠিকানা আপনি দেননি। ঠিকানা কী?”
শচীন ঠিকানা বলল। রেহান ঠিকানা টুকে নিল। পেনসিলটা হাতেই থাকল। “মিসেস বাপের বাড়িতে?”
“আজ্ঞে হ্যাঁ।”
“কত দিন?”
“মাস খানেক।”
“এর মধ্যে কোনো যোগাযোগ হয়নি?”
“আজ্ঞে সরাসরি নয়। ফোনে একবার হয়েছিল। শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলাম—পাত্তা পাইনি।”
“আপনার ম্যারেজ লাইফ চার বছরের?”
মাথা নাড়ল শচীন।
রেহান পেনসিল ফেলে দিয়ে এবার একটা সিগারেট ধরাল, লাইটার দিয়ে। “আপনার এগেনসটে কী কী কমপ্লেন মিসেসের?”
শচীন দুবার মাথা চুলকাল, কাশল বারকয়েক। “আজ্ঞে, কমপ্লেন তো হাজারো রকম। স্ত্রীরা স্বামীর বিরুদ্ধে কী না কমপ্লেন করে বলুন। ফ্রম এ টু জেড—!”
“স্বামীরাও করে, আপনিও করেছেন। কাজের কথা বলুন, ইউ মাস্ট টক বিজনেস, নাথিং এলস। আপনার মিসেস যে কমপ্লেনগুলো মেইনলি করতেন—বলুন!”
“মেইনলি! বলছি…! মেইন কমপ্লেন বলতে আমার বউ…”
“বউ নয়, স্ত্রী। সম্মান দিয়ে কথা বলুন। বউ বর এ সব ভালগার ওয়ার্ড ইউজ করবেন না।”
“আজ্ঞে বউ তো…।”
“প্লিজ স্টপ। কমপ্লেনের কথা বলুন।”
শচীন পকেট থেকে রুমাল বার করল। কপাল মুছল। বলল, “আমার স্ত্রীর মেইন কমপ্লেন হল—আমি স্ত্রৈণ নই।”
“স্ত্রৈণ! মানে আপনি স্ত্রীর বাধ্য ছিলেন না?”
“আজ্ঞে, কোনো কালেই নয়। স্ত্রী তো আমার জননী নয় যে বাধ্য হব!”
“আপনি বড় বাজে কথা বলেন।” বলেই রেহান বেল বাজালেন।
পাশের ঘর থেকে ফরসা বেঁটে ওজনদার এক মহিলা এসে দাঁড়াল।
রেহান বললেন, “সন্ধ্যা, জাস্ট সিট ডাউন। এই ভদ্রলোককে আমি তোমার কেয়ারে দিচ্ছি। তুমি কেসটা হ্যান্ডল করবে। এখন বসো, লিসন টু আওয়ার টকস। পরে ফাইলটা দেখে নিও। নিন, কমপ্লেনগুলো বলুন।”
শচীন সন্ধ্যা নাম্নী মহিলাকে দেখে নিল। সব দিকেই মানানসই। পছন্দই হল শচীনের। শচীন বলল, “আজ্ঞে আমার স্ত্রীর ধারণা, আমি ইরেসপনসিবল আমি আড্ডাবাজ। আমার মায়াদয়া নেই। আমি স্বার্থপর। স্ত্রীকে নাকি আমি ইগনোর করি। আমি নেশাখোর। আর লাস্টলি হল, আমি ইয়ে—মানে ফ্যামিলি ক্রিয়েট করছি না।” বলে শচীন অসহায় মুখ করল।
“বাচ্চা কাচ্চা না হবার কারণ?”
“ভগবান জানেন।”
“ডাক্তার দেখিয়েছেন?”
“সব রকম। সবাই আশা দিচ্ছে। কিন্তু…”
“বুঝেছি। তা আপনার কী কী গ্রিভান্স আছে স্ত্রীর বিরুদ্ধে?”
শচীন নিজে এবার সিগারেট খাবার জন্যে উসখুশ করতে লাগল। তারপর পকেট থেকে প্যাকেট বার করল সিগারেটের। “আমার গ্রিভান্স একটাই। আমার বউ—মানে স্ত্রী টু মাচ আদুরে। তার বাপের বাড়ি বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে মলয়ার। খুকি করে রেখে দিয়েছে।”
রেহান হাতের সিগারেট অ্যাশট্রেতে গুজে দিল। বলল, “অন্য কিছু না?”
“না, স্যার”, বলেই নিজেকে শুধরে নিল শচীন, “সরি ম্যাডাম।”
আবার পেনসিল তুলে নিয়ে দাঁতে টোকা দিল রেহান। “ডিভোর্সের প্রপোজালটা কার?”
“আমার স্ত্রীর!”
“তা ডিভোর্স যদি হয়—আপনার অসুবিধে কী?”
শচীন সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া গিলে বলল, “অসুবিধে কিছুই নেই তেমন। তবে আফটার অল চার বছর একসঙ্গে ছিলাম। ফাঁকা ফাঁকা লাগে। তা ছাড়া ভদ্রলোক একবারই বিয়ে করে। আমি আবার একটা বউ কোথায় পাব বলুন?”
রেহান বলল, “ঠিক আছে। আমরা দেখি কী করতে পারি।… ওই সন্ধ্যা আপনার কেস হ্যান্ডল করবে। আপনি ওর অ্যাডভাইস মতন চলবেন। ভাল কথা, সন্ধ্যার ঘোরাফেরা, এটা-ওটার কস্টও আপনাকে বিয়ার করতে হবে। সেটা আমাদের বিলে থাকবে না। আমরা পরে একটা বিল করব আপনাকে। অফ কোর্স ব্যাপারটা সেটল করতে পারলে।”
শচীন একবার সন্ধ্যার দিকে তাকাল।
রেহান বলল, “আমাদের চার্জটা?”
“ও! হ্যাঁ!” শচীন মানিব্যাগ খুলে পঁচিশটা টাকা বার করল।
টাকা নিল রেহান। “সন্ধ্যা, ওঁকে রসিদ দিয়ে দাও।”
প্রতাপরা অপেক্ষা করছিল বাড়িতে। শচীন আসতেই হর্ষধ্বনি করে উঠল।
“আয় আয়—হাঁ করে বসে আছি। কী হল?”
শচীন বলল, “দাঁড়া আগে দম নিই তারপর বলছি।”
গজেন তার চায়ের কাপটা এগিয়ে দিল শচীনকে। “নাও দাদা, চা খাও, তোমার গলা শুকিয়ে গিয়েছে।”
চা খেতে খেতে শচীন বিকেলের বৃত্তান্ত বর্ণনা করল।
সব শুনে সুবিমল বলল, “তোর তো ভালই হল রে? নাকের বদলে নরুণ পেলি। লেগে যা। উইশ উই বেস্ট লাক।”
সন্ধ্যা মেয়েটিকে বেশ পছন্দই হয়ে গেল শচীনের। অবশ্য সন্ধ্যা মেয়ে নয়, মহিলা। বছর বত্রিশ বয়েস। গোলগাল চেহারা। একটু ভারি গড়ন। গায়ের রং ফরসা। মুখটি হাসিখুশি মাখানো। বিবাহিতা। চট করে ধরা যায় না। স্বামী থাকে জাহাজে। মেরিনের লোক। ছ’ মাসে ন’ মাসে ঘরে ফেরে।
সন্ধ্যার আর সবই ভাল। বুদ্ধিমতী, স্মার্ট, জীবন্ত। কিন্তু বড় বেশি খাদ্যলোভী। শচীনকে নিয়ে যখন রেস্টুরেন্টে ঢোকে কম করেও দশ বারো টাকার খাদ্য একাই খায়। দুটো মোগলাই একসঙ্গে যদি বা সাঁটা যায়, তার সঙ্গে ডবল ডেভিল কেমন করে মানুষ হজম করে কে জানে। কাটলেট আর চপ একই সঙ্গে কেমন করে ওড়ায় মানুষ কে জানে! ভেলপুরি, চানা মটর তো হরদম হচ্ছে। মুহূর্মুহূ কোল্ড ড্রিঙ্ক। তার সঙ্গে ট্যাক্সি, সিনেমা।
শচীন হিসেব করে দেখল সাত দিনে সন্ধ্যার পিছনে তার প্রায় শ’ দুয়েক টাকা বেরিয়ে গিয়েছে। এইভাবে চললে কলসির জল তো ফুরিয়ে যাবে।
সেদিন বিকেলে মেট্রো সিনেমার কাছে দেখা হতেই সন্ধ্যা বলল, “আধঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রেখেছেন, ব্যাপার কী?”
“একটু দেরি হয়ে গেল। অফিসের কাজ।”
“আমার খিদে পেয়ে গিয়েছে। টিকিট কেটেছেন কুরবানির?”
“না, পারিনি।”
“জানতাম আপনি পারবেন না। আমি কেটে রেখেছি। নাইট শো।”
“নাইট শো।”
‘আটটা থেকে। আগে চলুন পেট ঠাণ্ডা করি। মার্কেটের রেস্টুরেন্টে যাব। বেড়াব খানিকটা, তারপর কুরবানি।”
শচীন বলল, “আজ আমার শরীরটা ভাল নেই। জ্বর জ্বর লাগছে।”
“ও ঠিক হয়ে যাবে। একটা স্যারিডনই যথেষ্ট। লেট আস গো।”
শচীন হিসেব করে দেখল, আজ তার অন্তত পঁচিশ ত্রিশ টাকা গচ্চা যাবে। উপায় নেই। পরের বউ বা অন্য মহিলা নিয়ে ঘোরাফেরা সত্যি বড় এক্সপেনসিভ। নিজের বউ এর ফিফটি পার্সেন্টও ছিল না। শচীনের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল।
রেস্টুরেন্টে খেতে বসে শচীন বলল, “ওদিকে আমার কতটা কাজ হল?”
“হচ্ছে।”
“হচ্ছে মানে?”
“কথাবার্তার চেষ্টা চলছে, সন্ধ্যা বলল ফাউল কাটলেট চিবুতে চিবুতে। “আপনার স্ত্রী ভীষণ অ্যাডামান্ট।”
“বলছে কী?”
“অনেক কথা। আপনি কোনো ভাবেই স্বামী হবার যোগ্য নয়।”
শচীন মাছ মাংসের দিকে যায়নি। পুডিং চা খাচ্ছিল। সন্ধ্যা আজ সিল্কের শাড়ি পরেছে, চন্দনের রং ব্লাউজটা একেবারেই খাটো, চুলের স্টাইল পালটেছে, দারুণ গন্ধ মেখেছে। শচীন বলল, “যোগ্য নয় বললে আমি আর কী বলব! আচ্ছা আপনিই বলুন—?”
“কী বলব?”
“না, আমার সঙ্গে মেশামেশিতে আপনার কী মনে হচ্ছে?”
সন্ধ্যা মুখ তুলে শচীনকে দেখল। চোখ ভরা হাসি। “আমার তো খুবই পছন্দ আপনাকে। ভীষণ।”
শচীন খুশি হল। “তা হলে? আপনার মতন মহিলা যদি পছন্দ করতে পারেন আমাকে আমার স্ত্রী কেন পারবেন না বলুন?”
সন্ধ্যা কাঁটা চামচ নামিয়ে দু হাত খোঁপার কাছে তুলে চুল ঠিক করল। হাসল। “সকলের পছন্দ এক নয়। আমি আপনাকে যতই দেখছি ততই ইমোশানালি অ্যাটাচড হয়ে পড়ছি। সত্যি! আমাদের যদি আগে দেখা হত…”
শচীন আহ্লাদে গলে গেল যেন। “কপাল! জীবনটা এই রকমই। যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাহি না…।”
“বাঃ! আপনি কবিতা লেখেন নাকি? কবিরা স্বামী হলে স্ত্রীদের কত আনন্দ—তাই না?”
শচীন সিগারেট ধরাল। “না আমি কবি নই। তবে আপনাকে দেখে মাঝে মাঝে পোয়ট্রি ফিল করি।”
সন্ধ্যা যেন খেলাচ্ছলে বুকের আঁচল সরিয়ে আবার শাড়ির ভাঁজ ঠিক করল। চাপা হাসি মুখে। “আমি জানি। আপনার চোখ বলে আপনি কী ফিল করেন। কিন্তু আমি কী ফিল করি আপনি বোঝেন?”
শচীন বলতে গিয়েও বলল না। তাকিয়ে থাকল।
সন্ধ্যা বলল, “পুরুষরা মেয়েদের কথা বোঝে না। আমরা কিন্তু আপনাদের কথা বুঝি।…নিন, এবার উঠব। আর ভাল লাগছে না। কুরবানিতে আমাদের সিট খুব ভাল।”
খানিকটা ঘোরাফেরা শেষ করে সিনেমা হলে।
সন্ধ্যার বাহাদুরি বলতে হবে। চমৎকার এক জোড়া সিট জোগাড় করেছে। একেবারে পিছনের সারি, ডানপাশের দেয়াল ঘেঁষা।
শচীন হিন্দি সিনেমার ভক্ত নয়। মাঝে মাঝে বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে যায়। রগড় দেখে আর হাসে।
সিনেমায় তার মন ছিল না। সন্ধ্যার সঙ্গে একটু খেলাখেলি করার ইচ্ছেই ছিল আসল। পায়ে পায়ে, কনুইয়ে কনুইয়ে, কাঁধে কাঁধে কিছুক্ষণ খেলাধুলো চলল, তারপর শচীন বলল, “আমার ঘুম পাচ্ছে। একটু ঘুরে আসি।”
‘ঘুম! এই রকম ছবি দেখা ছেড়ে?”
“আমার এই সময়ে একটু ঘুম-ঘুম পায়। বাইরে একটা চক্কর দিলে ঘুম কেটে যাবে। আপনি বরং ছবি দেখুন, আমি শোয়ের শেষে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকব।”
“ঠিক?”
“বিলকুল ঠিক।”
“আসুন তা হলে?”
শচীন বেরিয়ে গেল। বাইরে এসে ঘড়ি দেখল। হাতে ঘণ্টা খানেকেরও বেশি সময়। ব্রিস্টল থেকে দেড়খানা মেরে আসা যায়। আর দাঁড়াল না শচীন। হন হন করে ছোট ব্রিস্টলের দিকে এগুলো।
শচীন তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মুখে পান সিগারেট। চোখ সামান্য লালচে। সন্ধ্যা আসতেই শচীন হাত তুলল। “এই যে!”
কাছে এল সন্ধ্যা। শচীন বলল, “একটু তাড়াতাড়ি করুন। বৃষ্টি আসবে।”
“তাই নাকি? তা হলে ট্যাক্সি ধরতে হয়।”
“ধরা যাবে। আসুন।”
সন্ধ্যাকে নিয়ে ফাঁকায় আসতেই ট্যাক্সি পাওয়া গেল।
সন্ধ্যাকে উঠিয়ে শচীন উঠছে তার কানে এল কে যেন বলল, “শালার হেভি ব্ল্যাক মানি। সুখের পায়রা মাইরি। কেমন জুটিয়েছে।”
শচীন তাকাল। জনাপাঁচেক লোফার টাইপের ছোঁড়া।
ট্যাক্সি চলতে শুরু করলে শচীন বলল, “আমি একটা কথা ভাবছিলাম।”
“জানি” সন্ধ্যা বলল।
“জানেন? কী—?” শচীন গায়ে গায়ে বসল, একটা হাত সন্ধ্যার পিঠের ওপর দিয়ে ছড়িয়ে দিল। “কী জানেন?”
“আপনিই বলুন?”
“না, আপনি। মেয়েরা অনেক কিছু আগে বোঝে বলছিলেন না তখন? দেখি, কী বুঝেছেন আপনি?”
সন্ধ্যা খানিকটা ক্লান্তির ভাব করে আরও ডুবে গেল গদির মধ্যে। তার কাঁধে শচীনের হাত। রাস্তার দিকে তাকিয়ে সন্ধ্যা বলল, “ভাবছিলেন ডিভোর্সটা হয়ে যাওয়াই ভাল। তাই না?”
শচীন হাঁ হয়ে গেল। বলল, “একজ্যাক্টলি। আপনি কি থট রিডিং জানেন?”
“তা জানি। কিন্তু একতরফা যদি ডিভোর্স হয় লাভ কী? আমার তো মুক্তি নেই।”
“আপনিও করে নিন।”
“তার পর?”
“তারপর তো সবই সম্ভব। আমরা দুজনেই তখন মুক্ত।”
“না বাবা, আমার অত মুক্ত থাকতে ভাল লাগে না।”
“আহা—অত থাকবেন কেন? দু-এক মাস। তারপর আমরা যুক্ত হব।”
সন্ধ্যা শচীনের ঝোলানো এবং চঞ্চল হাত নিয়ে খেলা করতে লাগল। “মুখেই বলছেন। কাজের বেলায় তখন—?”
“না না মুখে বলব কেন! আমি মন থেকে বলছি।”
“যাঃ! মদ খেয়ে বলছেন?”
শচীন যেন বেজায় ধাক্কা খেল। বলল, “মাত্র দেড় খেয়েছি। এতে মাথা গোলমাল হয় না। যা বলছি একেবারে সজ্ঞানে।”
“সজ্ঞানে কেউ বোকা কথা বলে না,” সন্ধ্যা হাসল।
“মানে?”
“মানে আপনি আমার কেস। ক্লায়েন্ট। আপনার পরামর্শ শুনতে গেলে আমার কী দশা হবে! রেহানদি তাড়িয়ে দেবে আমায়। আমার চাকরি যাবে।”
“যাক। আমি চাই তোমার চাকরি যাক। কিসের পরোয়া তোমার! আমার সবকিছু তোমার।” বলে শচীন সন্ধ্যার কোলের ওপর ঢলে পড়ল।
সন্ধ্যা শচীনের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, “তুমি একেবারে নেংটি মাতাল। আমার এই নেংটি মাতালদের ভাল লাগে না। একদিন ধেড়ে মাতাল হয়ে কোলে শুয়ো তখন ক-ত আদর করব। নাও ওঠো। আর ন্যাকামি কোরো না।” বলে সন্ধ্যা চুলের ঝুঁটি ধরে শচীনকে তুলে বসিয়ে দিল।
জরুরি তলব রেহানের। টেলিগ্রাম হলে লেখা হত: কাম শার্প। ফোনে রেহান গম্ভীর গলায় বলল, “ছ’ টায় আসুন। জরুরি দরকার।”
শচীন বেশ ভয় পেল! দিন দুই আর দেখা নেই সন্ধ্যার। হয়তো অসুখ-বিসুখ করেছে। তার বাড়িটাও জানে না শচীন। জানবার চেষ্টা করেও পারেনি। সন্ধ্যা বলেছে, এটা আমাদের বলতে নেই। কনফিডেনসিয়াল। কী হবে বাড়ির ঠিকানা জেনে, ঠিকানার মানুষই তো হাজির।
শচীন এটাও লক্ষ করেছে, সন্ধ্যাকে যখনই ট্যাক্সি চাপিয়ে বাড়ি পৌঁছে দিতে গিয়েছে এলগিন রোডের মুখে এসে সন্ধ্যা বলেছে, আর নয়—এবার আপনি আসুন.’ একটা লোক এলগিন রোডের মুখ থেকে যে কোনো দিকে চলে যেতে পারে—সোজা ডাইনে বাঁয়ে—কাজেই সন্ধ্যা কোন দিকে যায়, কতটা যায়—তা শচীনের পক্ষে জানা সম্ভব নয়।
শচীন ভাবল প্রতাপকে একবার ফোন করে। করল না। করে লাভ নেই।
ঘড়িতে ছ’টা বাজার আগে আগেই শচীন রেহানের অফিসে গিয়ে হাজির। অন্যদের দেখল, সন্ধ্যাকে দেখতে পেল না।
রেহানের ঘরে ঢুকতেই দেখল, রেহান একেবারে সার্কাসের ড্রেস পরে বসে আছে। প্যান্ট, গেঞ্জি ধরনের জামা। হাতে সিগারেট।
শচীন প্রথমেই কেমন ভড়কে গেল।
“বসুন।”
বসল শচীন। রেহান টেবিল ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিল। দু মুহূর্ত চুপচাপ! তারপর বলল, “আপনি গত দু’ হপ্তা কী কী করেছেন—তার রিপোর্ট আমি দেখেছি। নাউ টেল মি, আপনার মোটিভটা কী?”
শচীন ঘাবড়ে গেল। “মানে?”
“মানে, আপনি কোন মতলব নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? আপনার স্ত্রীকে আপনি ফিরে পেতে চেয়েছিলেন—তাই না?”
“আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই।”
“আপনার স্ত্রী ডিভোর্সের মামলা আনছেন এই ভয়ে আপনি আমাদের কাছে ছুটে এসেছিলেন। আপনি চাইছিলেন, এই মামলা যেন তোলা না হয়। ইউ আর উইলিং টু গেট ব্যাক ইওর ওয়াইফ! কারেক্ট?”
শচীনের মনে হল, রেহান নিশ্চয় ল’ পাস করেছে, এবং প্র্যাকটিস করে। চমৎকার জেরা করছে। শচীন বলল, “হ্যাঁ, দ্যাটস রাইট।”
“মুখে রাইট বলছেন, কিন্তু কাজে কী করছেন?”
“কাজে। কেন, কাজে কী করব! আই ডিড নাথিং।”
“মিথ্যে কথা বলবেন না।” বলেই রেহান ফট করে টেবিলের ফড়িং টাইপের বাতিটা জ্বেলে দিয়ে হাতের কাছের ফ্ল্যাট ফাইল তুলে নিল। ফাইলটা তুলে নাচাবার ভঙ্গি করল—যেমন করে লোকে হাতের চাবুক নাচায়। “এখানে আপনার ডে টু ডে অ্যাকটিভিটি লেখা আছে নিন দেখুন—।’ রেহান ফাইলটা ছুড়ে দিল। দিয়ে ল্যাম্পটার মুখ ঘুরিয়ে দিল। “রিড ইট।”
শচীন রীতিমত ঘাবড়ে যাচ্ছিল। ফাইলটা খুলে নিয়ে পাতা ওল্টাল।
পাতা উলটে শচীন অবাক। সন্ধ্যা প্রতিদিনের রিপোর্ট পেশ করেছে বেশ গুছিয়ে। এরকম রিপোর্ট সামারি পেলে অফিসের বড়কর্তারা নিশ্চয় খুশি হতেন। কখন কোথায় দেখা হল, দেখা হবার পর কোথায় যাওয়া হল, কথাবার্তা কী হল, কেমন খাওয়া-দাওয়া হল—তার সমস্ত বিবরণ সংক্ষেপে লেখা।
শচীন এর কোনোটাই আপত্তি-যোগ্য বলতে পারে না।
“দেখলাম। কিন্তু আপনি যে বলেছেন আমি কিছু করেছি, কই, এখানে তা লেখা কোথায়?”
রেহান আবার একটা সিগারেট ধরাল। “করেননি?”
“না।”
“আপনি শেষ রিপোর্টটা দেখেছেন?”
“চোখ বুলিয়েছি।”
“দুজনে মিলে নাইট শোয়ে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন?”
“গিয়েছিলাম।” শচীন সাহস সংগ্রহের জন্যে একটা সিগারেট ধরাল।
“সিনেমা হলে আপনি—কী বলব—সন্ধ্যার হাত-টাত কাঁধ ধরেছিলেন?”
“ধরাধরির কী আছে মশাই! উনি টিকিট কেটেছিলেন নিজে। সিট দুটোও ভাল ছিল। চুপচাপ বসে সিনেমা দেখতে আমি পারি না। আমার একটু ইয়ে হয়…। আমি জাস্ট মজা করছিলাম।”
“মজা!… মজা ছেড়ে আপনি মদ খেতে বেরিয়ে গেলেন?”
“মজা ঠিক মতন করতে না পারলে বোর করে। আমার হাই উঠছিল, ঘুম পাচ্ছিল। সামান্য খেতে বেরিয়েছিলাম।”
রেহান হাত বাড়াল। ফাইলটা ফেরত নেবে। “সিনেমা থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে আপনি যা সব কাণ্ড করেছেন তা থেকেই বোঝা যায় আপনি তো একটা যাচ্ছেতাই ধরনের মানুষ।”
শচীন চুপ করে থাকল দু’মুহূর্ত, তারপর বলল, “কাণ্ড কিছুই করিনি। মানে তেমন কিছু!”
“করেননি! ইউ আর এ ড্যাম লায়ার! সন্ধ্যার হাত ধরে কী সব বলেছিলেন? ছি ছি, এদিকে আমাদের কাছে কাঁদুনি গাইতে এসেছেন, স্ত্রী যেন ডিভোর্স না করে, ওদিকে অন্য একজনের স্ত্রীকে উসকোচ্ছেন সে যাতে স্বামী ত্যাগ করে। তারপর…”
“আমি”, শচীন বাধা দিয়ে বলল, “কী বলেছি খেয়াল নেই। টু টেল ইউ ফ্র্যাংকলি খানিকটা নেশার ঘোরে ছিলাম। তবে হ্যাঁ, এটা বলেছিলাম, আমার তো কিছু হল না—আপনারও যা হাল—তাতে দুজনেই লেজ খসিয়ে পরে আবার ইয়ে করলে ভাল হয়।”
“ভাল হয়! আশ্চর্য! আপনি একজন পরস্ত্রীকে…”
“দেখুন! পরস্ত্রী-টরস্ত্রী জানি না। আমার গাঁটগচ্ছা কত যাচ্ছিল রোজ জানেন! বাড়িতে হিসেবের খাতায় লিখে রেখেছি।”
রেহান টেবিলের ওপর জোর থাপ্পড় মারল। “চুপ করুন। খরচার কথা তুলবেন না। আপনাকে বলাই হয়েছিল, সন্ধ্যার প্রফেশন্যাল এক্সপেন্সেস আপনাকে দিতে হবে। আপনি রাজি হয়েছিলেন।”
শচীন মাথা কাত করল। “হয়েছিলাম। তা বলে এত খরচ? মশাই খাওয়ার শেষ নেই। এক এক দিন চোদ্দো টাকার খাবার একাই খেতেন উনি। তার ওপর সিনেমা, ট্যাক্সি চড়ে হাওয়া খাওয়া…! আমাকে ফতুর করার জন্যে আপনি এই জিনিসটি আমার ঘাড়ে চাপিয়েছিলেন। তা আমি দেখলাম—পয়সা যখন যাচ্ছে তখন আমিই বা একতরফা খরচ করে যাই কেন শুধু শুধু, একটু রিটার্ন তো দরকার।”
রেহান বিকটভাবে চিৎকার করে উঠল, “রিটার্ন! দাঁড়ান রিটার্ন দেখাচ্ছি।” বলতে বলতে রেহান ঘণ্টি টিপল। ও-ঘর থেকে একজন এসে দাঁড়াল।
“সন্ধ্যাদের আসতে বল!”
শচীন কেমন ঘাবড়ে গেল। যাচ্চলে, সন্ধ্যাও আছে তা হলে? কোথায় ছিল সন্ধ্যা লুকিয়ে, শচীন তো দেখতে পায়নি!
রেহান হাত বাড়িয়ে ল্যাম্পটা টেনে নিজের দিকে করে নিল।
শচীন বলল, “একটা কথা বলব?”
“বলুন?”
“আমি আপনাদের অ্যায়সা প্যাঁচে পড়েছিলাম যে প্যাঁচ কেটে বেরুবার উপায় পাচ্ছিলাম না। ইচ্ছে করেই ওসব করেছি।”
“আমরা আপনাকে প্যাঁচে ফেলেছিলাম?”
“দারুণ প্যাঁচে ফেলেছিলেন। বউ ফিরিয়ে দেবার লোভ দেখিয়ে এক্সপ্লয়েট করছিলেন। আপনারা…”
শচীনের কথা শেষ হল না, দরজা খুলে সন্ধ্যা এল; সঙ্গে আর-এক মহিলা।
শচীন তাকিয়ে দেখল। তারপর তার ধাত ছেড়ে যাবার জো। মলয়া। একেবারে জ্বলজ্যান্ত। শচীনের গলা শুকিয়ে গেল।
রেহান সন্ধ্যাদের দেওয়াল-ঘেঁষা সোফায় বসতে বলল। তারপর শচীনের দিকে তাকাল। “আপনি বলছিলেন, আমরা আপনাকে প্যাঁচে ফেলেছি। তা খানিকটা ফেলেছি অবশ্য। যে রিপোর্টগুলো আপনি দেখলেন, তার একটা করে কপি আমরা সব সময় আপনার স্ত্রীকে পৌঁছে দিয়েছি, টু ইনফর্ম হার অ্যাবাউট ইওর মিসডিডস!”
শচীন ঘামতে লাগল। এ তো সর্বনেশে জায়গা রে বাবা!
রেহান সন্ধ্যাদের দিকে তাকাল। মলয়াকে বলল, “ভাই, এবার আমি তোমাকে ওই স্বামী নামক মানুষটির কিছু কথাবার্তা শোনাব। প্লিজ লিসন।” বলে রেহান কোথায় একটা কল টিপল। তারপর শোনা গেল শচীনের গলা।
শচীন চমকে উঠেছিল। তারপর বুঝতে পারল রেহান আজকের কথাবার্তা কায়দা করে টেপ করে নিয়েছে। টেবিল ল্যাম্পটার দিকে তাকাল শচীন। তার একবারও মনে হয়নি, ওটা শুধু বাতি নয়, আর-এক গেঁড়াকল।
রেহানের টেবিলের আড়াল থেকে টেপ বাজতে লাগল।
আর শচীন বসে বসে ঘামতে লাগল।
শেষকালে টেপ শেষ হল।
একেবারে চুপচাপ।
রেহান বলল, “ভাই মলয়া, এই তোমার স্বামী। নিজের কানেই সব শুনলে। তুমি কি ওঁর কাছে ফিরে যেতে চাও? না কি ডিভোর্স স্যুট ফাইল করবে? আমরা তোমার তরফে সাক্ষী দিতে পারি। রেডি ডকুমেন্ট আছে।”
সন্ধ্যা বলল, “আমি কোর্টে আরও অনেক কিছু বলব। মোস্ট আনফেথফুল হাজবেন্ড। তুমি ডিভোর্স পেয়ে যাবে।”
শচীন চিৎকার করে বলল, “এ-সব কী হচ্ছে! বাঃ! আমি বউ ফেরত পাবার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছি—আর আপনারা ব্যাপারটা কাঁচিয়ে দিচ্ছেন!”
রেহান বলল, “আপনি কি স্ত্রী ফেরত পাবার যোগ্য?”
“তার মানে!” শচীন আসামীর মতন মলয়ার দিকে তাকাল। “আমার এখানে আসার উদ্দেশ্যটা কী ছিল বলুন? স্ত্রীর জন্যেই এসেছিলাম। শালীদের জন্যে নয়।”
রেহান থ। তারপরই গর্জন। “কী বললেন, শালী!”
শচীন বলল, “স্ত্রীর বোনরা শালীই হন। বাংলা মতে। …নিন, অনেক হয়েছে, আর আমায় ঘাঁটাবেন না।” বলে শচীন মলয়ার দিকে তাকাল। “তুমি তোমার দিদিদের সব কথা বিশ্বাস কোরো না, প্লিজ। যা করেছি তোমার জন্যে। ঘরে চলো লক্ষ্মী! পা ধরব?”
সন্ধ্যা খিল খিল করে হেসে উঠল।
রেহানও হাসছিল। হাসতে হাসতে বলল, “মলয়া, এমন লেজকাটা ভগ্নিপতি আমি দেখিনি ভাই। তা যা করার তোমরাই ঠিক করো। এই মশাই, বউ নিয়ে যান আর না-যান আমাদের পুরো ফিজ কিন্তু দিয়ে যাবেন।”
ট্যাক্সিতে পাশাপাশি বসে শচীন বলল, “তুমি আমার বাইরে বাইরে চিনলে ভাই, ভেতরটা দেখলে না?”
মলয়া কথা বলল না।
শচীন স্ত্রীর হাত টেনে নিয়ে বলল, “তোমার প্রাণে একটু মায়া নেই। চার বছরের স্বামী। দেড় মাস তাকে খেলালে?”
মলয়া বলল, “মায়া-টায়া জানি না। তবে খুব খেলছিলে। তোমার খেলার কথা শুনে গা আমার রিরি করত, বাড়ি চলো—খেলা দেখাব।”
শচীন বউয়ের কোলে হাত ডুবিয়ে বলল, “নিশ্চয়ই দেখাবে। তোমার খেলা না দেখে মরে যাচ্ছিলাম মাইরি।”
মলয়া স্বামীর হাত সরিয়ে দিয়ে বলল, “অসভ্যতা কোরো না।”
বসন্ত বিলাপ
অতি তুচ্ছ ঘটনা থেকে অনেক বৃহৎ কাণ্ড ঘটে যায়। শ্যামের বেলায়ও ব্যাপারটা সেই রকম ঘটেছিল। রেল স্টেশনের বাইরে সিঁড়ির কাছে শ্যাম দাঁড়িয়ে ছিল। মুখে প্রায় ফুরিয়ে-আসা সিগারেট। ভিড়টিড় বলতে আশপাশে তখন বিশেষ কিছু ছিল না, শাট্ল্ ট্রেনের যাত্রীরা সকলেই চলে গেছে একরকম। শ্যাম সামনের দিকে তাকিয়ে একটা সাইকেল রিকশা খুঁজছিল। কিন্তু সে বেশ অন্যমনস্ক ছিল। অন্যমনস্কতার মধ্যেই শ্যাম দূরের একটা রিকশাকে ডান হাত তুলে ইশারায় কাছে ডাকল, এবং অন্যমনস্কভাবেই বাঁ হাতের আঙুলের টোকায় সিগারেটের অতিক্ষুদ্র অংশটা বাঁ দিকে ছুড়ে দিল। শ্যাম সামনের রিকশা দেখছিল—আপপাশ দেখেনি। রিকশার জন্যে শ্যাম এগুতে যাচ্ছে, আচমকা তার জামা ধরে কেউ বেজায় জোরে টান মারল। মুখ ফিরিয়ে শ্যাম দেখল ‘বসন্ত বিলাপ’-এর সেই সিংহবাহিনী, পাশে তার অন্য এক সঙ্গিনী।
একেবারে প্রথমটায় শ্যাম কিছু না বুঝে চমকে ওঠার মতন হলেও পরের কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে সব বুঝে নিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। তার সিগারেটের টুকরোটা মেয়েটির—অর্থাৎ সেই সিংহবাহিনীর শাড়ির সামনের কুঁচির মধ্যে ছুঁছো বাজির মতন ঢুকে গিয়েছিল। স্টেশনের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, দিবালোকে শাড়ির পায়ের কাছটা দুলিয়ে, নাচিয়ে, কিছুটা বা সামনে বাড়িয়ে মেয়েটি অগ্নিমূর্তি হয়ে শ্যামকে সগর্জনে ধমকাতে ও গালিগালাজ করতে শুরু করল। মেয়েদের আরক্ত মুখ, রাঙা চোখ, সকুঞ্চিত ভ্রূ স্ফুরিত নাসা, দস্তপঙ্ক্তি—কোনোটাই শ্যামের অপ্রিয় বস্তু নয়, কেননা শ্যামের মাত্র চৌত্রিশ বছর চলছে, সে একটু-আধটু শৌখিন কাব্যচর্চাও করে থাকে এবং এখনও অবিবাহিত। কিন্তু এই মুহূর্তে শ্যাম চোখে অন্ধকার দেখছিল, তার সম্মুখস্থ মেয়েটির তর্জন-গর্জনে তার হুঁশ প্রায় ছিল না, আর গালিগালাজ যেটুকু মরমে প্রবেশ করছিল তাতে অপমানে শ্যাম একেবারে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যাচ্ছিল।
ইডিয়েট, অসভ্য, জন্তু অভদ্র—ইত্যাদি শব্দগুলি ছুরির মতন শ্যামের আত্মসম্ম নে যত্রতত্র বিদ্ধ হলেও সে শুধু তোতলাবার চেষ্টা করছিল, কথা বলতে পারছিল না। অবশেষে মেয়েটি যখন শ্যামকে বাঁদর বলল এবং শ্যামের কান ধরে ছিঁড়ে দেবার অভিপ্রায় জানিয়ে কান ধরার একটা ভঙ্গিও করল, তখন শ্যাম আর সহ্য করতে পারল না। বলল, “এটা ইন্টেনশনাল নয়।”
সঙ্গে সঙ্গে আরও গর্জন করে মেয়েটি বলল, “নিশ্চয় ইন্টেনশনাল। চিনি না আপনাদের। যত ফেউয়ের দল।”
অগত্যা শ্যাম চুপ। কিছু লোকজন, মুটেমজুর জমে গেছে আশপাশে।
অবশেষে সঙ্গিনীকে টেনে নিয়ে গিয়ে সিংহ বাহিনী সামনের রিকশায় উঠল। শ্যামেরই ডাকা সেই রিকশাটা। যাবার সময় মেয়েটি গলা বাজিয়ে বলে গেল “এ-রকম নচ্ছারদের ধরে নিয়ে গিয়ে পুলিশে দিতে হয়। যত সব বাঁদর।”
শ্যাম অসহায়ের মতন দাঁড়িয়ে থাকল, তার অবস্থাটা বজ্রাহতের মতন।
কী দুর্দৈব। শ্যাম ভদ্রলোক। সে অশিক্ষিত, বেকার, বকাটে নয়। তার চেহারা বা চালচলনে বাঁদরামি করার কোনো লক্ষণ নেই। পুলিশে দেবার মতন লোক শ্যাম নয়। সেই শ্যামকে আজ এই হাটের মধ্যে মেয়েটা অপমানের একশেষ করে গেল! ছি ছি! শ্যাম শুধু আহত হল না, বেচারির চোখে প্রায় জল এসে গেল।
সন্ধেবেলায় শ্যাম বিরক্ত, বিমর্ষ ও উত্তেজিত হয়ে তাদের আড্ডায় এসে বলল, “সিধু, আমি সুসাইড করব।”
সিধু চওড়া চৌকির ওপর পাতা মোটা সতরঞ্চির ওপর কাত হয়ে শুয়ে ফুটবলের লীগ টেবল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল। দত্তগুপ্ত একটা তাকিয়া মাথায় দিয়ে শুয়ে শুয়ে কড়ি কাঠ দেখতে দেখতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সুর ভাঁজছিল নিচু গলায়। আর ললিত—এই বাড়ির হাফ-মালিক—তাস, কাগজ-কলম বের করে নিচ্ছিল।
শ্যামের প্রবেশ এবং ক্ষোভ প্রকাশ বন্ধুদের তেমন উৎসাহ সঞ্চার করল না। সিধু লীগ টেবল থেকে মনে মনে একটা অঙ্ক কষতে লাগল, দত্তগুপ্ত নির্বিকারচিত্তে সুর সাধনা করে যেতে থাকল।
ললিত শুধু বলল, “কি করবি?”
“সুসাইড।”
“বাঃ! ভাল জিনিস! জাপানিরা হরদম করে।”
বন্ধুদের এরকম পরিহাস, ঠাণ্ডা মনোভাব শ্যাম বরদাস্ত করতে পারল না। চৌকিতে না বসেই শ্যাম বার দুই পায়চারি করল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর তিক্ত গলায় বলল, “আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে! লাইফে এরকম বেইজ্জতি আর হইনি।…বসন্ত-বিলাপের সেই মেয়েটা—সিংহবাহিনীটা পাবলিক প্লেসে দাঁড়িয়ে আমার ইনসালট করেছে। আমার কান ধরে ছিঁড়ে দেবে বলেছে। …” শ্যাম আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, দম নেবার জন্যে, থেমে গেল!
বসন্ত বিলাপের নামেই হোক বা সিংহবাহিনীর টানেই হোক সিধু এবার মুখ ওঠাল। ললিত ভাল করে নজর করতে লাগল শ্যামকে। সুরচর্চা থামিয়ে দত্তগুপ্ত উঠে বসতে বসতে বলল, “কস্ কি রে শ্যাম? মাইয়া মাইনষে তরে ইনসালট্ করল?”
ললিত বলল, “ব্যাপারটা কি?”
সিধু পকেট থেকে পানের মোড়কটা বের করে পাশে রাখল। বলল, “তোকে বেইজ্জত করল কেন? চোখফোক টিপে ছিলি নাকি?”
শ্যাম আগুন হয়ে উঠল। “হোয়ট ডু ইউ মিন্? আমি কি শালা লোফার না লোচ্চা?”
হেসে উঠে সিধু বলল, “তুই চটছিস কেন? আমি কি গাল টেপার কথা বলেছি! চোখ টেপা কোনো ক্রাইম নয়। আয়, বোস, কি হয়েছে বল সব…”
বন্ধুরা এবার আর ঠাণ্ডা থাকতে পারল না, রীতিমত চঞ্চল হয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠল।
দত্তগুপ্ত স্কুলে পড়ার সময় কোথায় যেন বক্সিং শিখেছিল, ঘুঁষি পাকিয়ে বলল, “একটা গুসি দিলি না ক্যান?’
এমন সময় ললিতের বউদি মণিমালা ভেতরের দরজা দিয়ে আবির্ভূত হল। মণিমালার বয়স বেশি নয়, ললিতের সমবয়সীই হবে হয়ত, এবং এই আড্ডার চার আনা সদস্য। অর্থাৎ সে এখানকার গল্পগুজবে কখনো-সখনো থাকে, এবং মাঝে মাঝে তাস খেলায়। পরিবর্তে তাকে এই চার দেবরকে চার এবং মাঝেমধ্যে খাবার-টাবার খাওয়াতে হয়।
মণিমালা বরাবরই হাসিখুশি মানুষ। তামাশা রসিকতায় কিছু কম যায় না। দেখতে সুশ্রী, সামান্য গোলগাল ধরনের চেহারা।
মণিমালা এসে বলল, “কি, এখনও তাস পাড়োনি?”
শ্যামরা কেউ কোনো জবাব দিল না।
মণিমালা চার জনের ভাবসাব দেখতে লাগল।
সামান্যা পরে ললিত বলল, “আজ আমরা তাস খেলছি না। …একটা ব্যাপার ভাবছি। তুমি বরং স্ট্রং করে চা পাঠিয়ে দাও।”
মিণমালা যেন কোনও কিছুর গন্ধ শুঁকতে পেল। সন্দিগ্ধ গলায় বলল, “তা ব্যাপারটা কি শুনতে পারি না?”
বন্ধুদের মধ্যে চোখাচোখি হবার আগেই দত্তগুপ্ত বলল, “শ্যামচাঁদের কান…।” কথাটা দস্তগুপ্ত শেষ করতে পারল না, তার আগেই শ্যাম জোরে একটা কনুইয়ের গুঁতো দিল গর্দভটাকে। উঃ শব্দ করে দত্তগুপ্ত থেমে গেল।
ললিত বলল, “ব্যাপারটা এখন তোমায় বলতে পারছি না। …না কি রে? কি বলিস ?” ললিত বন্ধুদের দিকে চোখ ছোট করে তাকাল। “পরে বলব। একটু চা-ফা খাওয়াও আগে।”
মনিমালা শ্যামের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। হেসে চলে গেল।
মিণমালা চলে যেতেই শ্যাম দত্তগুপ্তকে খেঁকিয়ে উঠল, “রাস্কেল কোথাকার! এখুনি ডুবিয়ে ছেড়েছিল! বউদির কাছে তুই আমার বেইজ্জতির কথা বলছিলি! কেলেঙ্কারী হয়ে যেত।”
দত্তগুপ্ত বলল, “বউদিরে কইতে দোষ কি?” সে বলল বটে, কিন্তু তার বোকামিটা বুঝতে পেরেছিল।
সিধু বলল, “দোষ কিছু নয়, প্রেস্টিজ আরও পাঞ্চার হত।”
ললিত বলল, “বাজে কথা থাক। এখন কি হবে? লেট আস ডিসাইড। ব্যাপারটা এভাবে ছেড়ে দেওয়া যায় না। স্পেশ্যালি বসন্ত বিলাপের সঙ্গে আমাদের এটা থার্ড রাউন্ড। আগের দু’বার মেয়েছেলে বলে ছেড়ে দিয়েছিলাম। বাট নট দিস টাইম।”
আগের দু’বার—অর্থাৎ একবার বসন্ত বিলাপের বাড়ি থেকে একরাজ্যি ময়লা সিধুর মাথার ওপর ফেলে দেওয়া হয়েছিল। অন্যবার—অবশ্য সেটা প্রত্যক্ষ নয় পরোক্ষভাবেই বসন্ত বিলাপ ললিতদের বেইজ্জত করেছিল, সরস্বতী পুজোর নিমন্ত্রণপত্র বলে ডাক মারফত ঠিকানা লেখা খাম পাঠিয়ে দিয়েছিল, ভেতরে কার্ড বা ছপা চিঠি কিছু ছিল না।
দত্তগুপ্তর কাছ থেকে একটা সিগারেট চেয়ে নিয়ে সিধু ততক্ষণে ধরিয়ে ফেলেছে। লম্বা ধোঁয়া ছেড়ে বলল, “না, আর টলারেট করা যায় না। আমাদের স্ট্রেট ফাইট দিতে হবে।”
-দত্তগুপ্ত রসিকতা করে হেসে বলল, “ফাইটে কাম্ নাই রে, টাইটেই চলব।”
শ্যাম ধমক দিয়ে বলল, “ডোন্ট লাফ্, এটা হাসির ব্যাপার নয়।”
দত্তগুপ্ত একান্ত অনুগতের মতন মুখভাব গম্ভীর করে নিল।
অতঃপর চার বন্ধু গভীর মনোযোগ সহকারে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে বসল।
বসন্ত বিলাস সম্পর্কে এবার কিছু বলতে হয়। সংক্ষেপে বললে এই দাঁড়ায় যে, ললিতদের পাড়ায়, এমন কি এই রাস্তার ওপরই বসন্ত বিলাপের অবস্থান। বেশি নয়, এই বাড়ি থেকে মাত্র মিনিট দুই হাঁটলেই বাড়িটা দেখা যায়। লালচে রঙের ছোটাখাটো দোতলা বাড়ি একটা, নিচে উপেন স্যাকরার দোকান। উপেনের পাশে অবশ্য হোমিও ডাক্তার গিরিজাবাবুর ডিসপেনসারি। আজ প্রায় বছর খানেক হতে চলল, কয়েকটি মেয়ে এসে ওই বাড়িটা ভাড়া নিয়ে একটা মেয়ে-মেস বা মেয়ে-হোস্টেল তৈরি করে দিব্যি আছে। হই-হল্লা, চেঁচামেচি করে, নেচে গেয়ে বেশ আছে সব। মনেই হয় না মেয়েদের বয়েস হয়েছে। সবাই চাকরি-বাকরি করে। কেউ বা রেলে; কেউ মেয়ে কলেজে, কেউ বা হাসপাতালে। স্কুলে চাকরি করা মেয়েও আছে জনা দুই-তিন। সবচেয়ে আশ্চর্য এই মেয়েদের মধ্যে বিবাহিত বলতে মাত্র একজন, প্রতিমা, হাসপাতালের মেট্রন ; বয়স একটু বেশিই হবে। অন্য কোনো মেয়ের মাথাতেই এখন পর্যন্ত সিঁদুরের দাগ ধরেনি।
বাড়িটার একটা নম্বর আছে কিন্তু নাম নেই। নামটা শ্যামদের দেওয়া, শ্যামেরই। জনা, আট-দশ ,মেয়ে যে বাড়িতে থাকে, এবং যেখানে সকলেই প্রায় কুমারী, সেই বাড়ির নাম বসন্ত বিলাপ হলে খুব বেমানান নিশ্চয় হয় না। শ্যামের যুক্তিতে, এতগুলি যুবতীর কৌমার্য অবলম্বন—বসন্তের বিলাপ ছাড়া আর কিই বা! শ্যাম এবং শ্যামের বন্ধুদের কাছে আজ বছর খানেকই বসন্ত বিলাপ প্রবল কৌতূহল ও রহস্যের বিষয়। এই এক বছরে বসন্ত বিলাপের পরিবর্তন অল্পস্বল্প হয়েছে, নতুন কেউ এসেছে পুরনো কেউ চলে গেছে, ওদের ঝি বদলেছে—তবু মোটামুটি চেহারাটা সেই রকমই আছে। আর শ্যামরা বসন্ত বিলাপের অধিবাসীদের নাম ধাম, কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকাকিবহাল। মেয়ের রূপগুণ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিচার করে তারা আবার নিজেদের মধ্যে এক-একজনের এক-একটা নামও দিয়ে নিয়েছে। যেমন সিংহবাহিনী। সিংহবাহিনীর আসল নাম অনুরাধা সিংহ, বয়স বছর ত্রিশের সামান্য বেশি বলেই মনে হয়, মাথায় সামান্য খাটো, বেশ পুষ্ট চেহারা, মেজাজ খুব কড়া ধরনের, রাস্তা দিয়ে হাঁটার, সময় মিলিটারী মেজাজে হাঁটে, গলার স্বর থেকে মনে হয় ভগবান যেন তার আলজিভের কাছে একটি বিশেষ ধরনের টিনি-মাইক লাগিয়ে দিয়েছে ! চালচলনে ব্যবহারে যার এত দাপটের ভাব তাকে দত্তগুপ্ত ‘মহিষমর্দিনী’ বলতে চেয়েছিল, কিন্তু শ্যাম বা ললিত এতটা নির্দয় হতে রাজি হয়নি; বরং অনুরাধা সিংহকে সিংহবাহিনী বলাই সঙ্গত, তা ছাড়া এটা তো ঠিকই মেয়েটিকে তার চারিত্রিক সিংহই তো বহন করছে।
মণিমালা চা নিয়ে এসে ললিতদের কাছে একটা বেতের মোড়া টেনে নিয়ে বসল।
ললিত প্রথমে হালকাভাবে বলল, “দাদা কোথায়?”
“কোথায় আর—যেখানে যার দৌড়—কোলিয়ারির এক মক্কেল এসে নিয়ে গেছে।”
সিধু চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, “আজ পল্টনকে একবারও তো দেখলাম না বউদি? কোথায় গেছে?”
মণিমালা হেসে বলল, “আজ বাপের সঙ্গে গেছে। যা বায়না!”
শ্যাম, ললিত, দত্তগুপ্তের মধ্যে গোপনে চোখ চাওয়া-চাওয়ি হয়ে যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ললিত গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল, “বউদি, আমরা একটা সিরিয়াস ম্যাটার নিয়ে আলোচনা করছিলাম। ব্যাপারটা খুব সিক্রেট।…এখন ব্যাপার হচ্ছে কি, মানে—তুমি এমন এক পার্টি—না ঠিক পার্টি নয়—ধরো সম্প্রদায়ের লোক যার কাছে আমরা—পুরুষরা কিছু বলতে পারি না। ব্যাপারটা মেয়েদের নিয়ে। তবু তোমায় আমরা বলব। তোমাকে কনফিডেন্সে নেওয়া গেল।”
মণিমালা ঘাড় হেলিয়ে বলল, “বড় ভনিতা করছ। ব্যাপারটা বললা শুনি।”
শ্যাম বলল, “আপনি আমাদের দলে, এটা কিন্তু প্রমিস করতে হবে।”
মণিমালা সঙ্গে সঙ্গে মাথা দুলিয়ে তিন সত্যি করল।
ললিত বলল, “ব্যাপারটা বসন্ত বিলাপ নিয়ে। আজ সেই সিংহীটা শ্যামকে দশজনের সামনে যাচ্ছেতাই করে অপমান করেছে। আমরা এর শোধ নেব।”
দত্তগুপ্ত ইংরিজি করে বলল, “রিভেনজ। বুজলেন না বউদিদি, সিংহীরে টাইট রমু।” দত্তগুপ্তর বাড়ি কোনো কালেই পূর্ববঙ্গে ছিল না, অথচ সে এইভাবে কথা বলে, এটা নিছক রঙ্গ করেই। বাড়িতে তার নিজের বউদিদিও পূর্ববঙ্গীয়, দাদা খাস শান্তিপুরি বাঙলায় কথা বলে। নিতান্ত যেন বউদিদিকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে দত্তগুপ্ত ল্যাংগুয়েজ ক্লাসের মতন পূর্ববঙ্গীয় ভাষাটা রপ্ত করছে।
স্টেশনের ঘটনাটা সিধু সংক্ষেপে বলল। শুনতে শুনতে মণিমালা হেসে অস্থির।
শ্যাম ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, “বউদি আপনি হাসছেন, ব্যাপারটা কিন্তু হাসির নয়। আমি সত্যিই বড় অপদস্থ হয়েছি।”
মণিমালা আঁচলের আগায় মুখের বেশি হাসিটা মুছে খানিকটা শান্ত হয়ে বলল, “সত্যিই ভাই, ব্যাপারটা খারাপ। কিন্তু আপনিই বা অত কথা শুনলেন কেন, দু’-চারটে বলে দিলে পারতেন।”
“পাগল! তা হলে সিংহবাহিনী শ্যামের কান কেটে ছেড়ে দিত।” সিধু বলল, ‘রিট্রট ইন ডেনজারই বেস্ট পলিসি।”
ললিত সকলকে থামিয়ে দিয়ে মণিমালাকে বলল, “আমরা একটা প্ল্যান করে ফেলেছি। এটায় আনসাকসেসফুল হলে অন্য পথ বেছে নেব। আমাদের প্ল্যানটা তুমি শুনবে?”
“বলো, শুনি।”
ললিত তাদের মতলবটা বলল।
শুনে মণিমালা শান্ত মিষ্টি হাসি হেসে বলল, “ও-সব ছাই কোনো আসবে না। বাড়িটার গায়ে শুধু দাদের মতন দাগ হবে। তা ছাড়া পাড়ার পাঁচ জনের চোখে পড়বে, তোমরাও ধরা পড়বে।”
সিধু বলল, “কিন্তু বউদিদি, পোস্টারিংটা খুব এফেকটিভ হবে। আমরা শুধু ছড়া লিখব। কিংবা সিনেমার কিছু হাল কায়দার বিজ্ঞাপনের মতন প্রথম দিন শুধু এক লাইন যেমন ‘একটি দুরন্ত আকর্ষণ; পরের দিন আরও এক লাইন “নয়ন সার্থক”।
মণিমালা মাথা নাড়ল, “না না, এসব কি?”
“তাহলে ছড়া?…শ্যাম লিখবে। আমরা ফুলস্কেপ কাগজে রঙিন কালি দিয়ে বেশ ডিজাইন করে চন্দরকে দিয়ে লিখিয়ে নেব।”
“দেওয়ালে আঁটবে কে?”
“পয়সা দিলে কাগজ আঁটার লোক পাওয়া যায়।”
“তা যাক্। এটা কিন্তু খারাপ…। এভাবে কারও পেছন লাগা ভাল নয়।”
“এই তো তুমি তোমার কমিউনিটির ইন্টারেস্ট দেখতে লাগলে—” ললিত বলল, “শ্যামের বা আমাদের পেছনে লাগতে বসন্ত বিলাপের মেয়েদের তো খারাপ লাগেনি। গোলমালটা ওরা পাকিয়েছে, আমরা নয়।”
মণিমালা ওদের মাথা ঠাণ্ডা করার জন্যে নরম গলায় বলল, “কে কার পেছনে লেগেছে সেটা অন্য কথা। তা হলে তোমরা মেয়েদের পেছনে এভাবে লাগবে কেন? অন্যভাবে লাগ?”
“অন্যভাবে লাগা মানে তো ঢিল ছোঁড়া?” শ্যাম অপ্রসন্ন গলায় বলল।
“দু চারটে বোমাও মারা যায়—কিন্তু সেটা কি উচিত হবে। আমরা ভদ্দরলোকের মতন অহিংস সংগ্রাম করতে চাই। ওদের ঝাড়সুদ্ধু এ পাড়া থেকে ওঠাতে চাই। বেজায় পাজি হয়ে গেছে—সব ক’টা। জটলা করে দাঁড়ায়, দোতলার বারান্দা থেকে মুখ বাড়িয়ে টিটকিরি মারে। আমাদের বাঁদর-টাঁদরই ভাবে।” ললিত বলল।
মণিমালা যথেষ্ট চালাক। আবহাওয়া বুঝে নিয়ে বলল, “তোমরা লাগতে চাও লাগো। তবে, আমি বলছিলাম কি, খুব চুপচাপ—কাউকে কিছু জানতে না দিয়ে পেছনে লাগো।”
চার বন্ধুই একসঙ্গে বলল, “কি রকম?”
মণিমালা জবাব দিল না।
ললিত বলল, “তোমার আইডিয়াটা কি রকম?”
“দাঁড়াও ভাবি একটু।”
মণিমালা ভাবতে লাগল। চার বন্ধুই মণিমালার মুখের দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল নীরবে।
শেষ পর্যন্ত মণিমালা বলল, “আমি একটা উপায় ভেবেছি।”
“কি?”
মণিমালা তার উপায়টি ব্যক্ত করল। সঙ্গে সঙ্গে নানা জটিল প্রশ্ন। মণিমালা সব প্রশ্নেরই জবাব দিল যতটা সাধ্য।
দেখা গেল মণিমালার সিদ্ধান্ত ওরা মেনে নিয়েছে।
২
সপ্তাহ দুই পরে সিধুই একদিন নাচতে নাচতে এসে বলল, “লেগেছে রে, লেগেছে।”
ললিত যদিও আঁচ করতে পারল, তবুও শুধলো, “কি লেগেছে?”
“হুলুস্থুল। বসন্ত বিলাপে ফায়ার লেগে গেছে।”
শ্যাম হাতের কাগজটা ফেলে দিয়ে সহর্ষে চিৎকার করে উঠল, “লেগে যাক—লেগে যাক ; লাগিয়ে দে মা জগদম্বা…”
দত্তগুপ্ত বলল, “ফায়ার স্প্রেড করলে আমারে কল দিস রে সিধু।”
বাইরে আজ বিকেল থেকে খানিকটা ঝোড়ো ভাব হয়েছে। আকাশে মেঘ জুটেছে দুপুর থেকে, বৃষ্টি নেই, মাঝে মাঝে মেঘ ডেকে উঠেছে। হয়ত মাঝ রাত থেকে বৃষ্টি নামবে।
ললিত সিধুকে জিজ্ঞেস করল, “লেগেছে তুই বুঝলি কি করে?”
“সিকরেট মিশন ভাই; বলেছিলাম না—আমি ওটা ক্যাচ করে ফেলব।…এইবার জমবে।”
“বউদিকে ডাক—” শ্যাম অধৈর্য হয়ে বলল, “ডাক বউদিকে, ললিত। শীঘ্রি।”
ললিতকে উঠতে হল না, দত্তগুপ্তই উঠে ভেতর দরজায় গিয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মণিমালাকে ডাকল।
সিধু বলল, “আমি ভাবছি আর-একবার ওষুধটা রিপিট করে দেওয়া যাক। প্রথমটাতেই বেশ ধরেছে যখন তখন রিপিট করলে আরও ফার্স্ট ক্লাস হবে। কি বল?”
শ্যাম বলল, “গুড আইডিয়া। এবার ডোজ আরও একটু কড়া করে দেওয়া যেতে পারে।”
ললিত বলল, “তাহলে এবার শ্যামই খরচটা দিক।”
“আমি একলা কেন?” শ্যাম আপত্তির গলায় বলল।
“তোর জন্যেই এই লড়াই। তোকে নিয়েই আমাদের লড়তে হচ্ছে। তুই শালা চ্যাম্পিয়ন হবি।”
শ্যাম কি যেন ভেবে বলল, “আমার একলার সঙ্গে লড়াই হচ্ছে না, হচ্ছে আমাদের সঙ্গে; তা হলেও তোরা বলছিস যখন আমি দেব, টাকা দেব।…যা অপমান সয়েছি সেদিন।”
সামান্য পরেই মণিমালা এল।
মণিমালা আসতেই সিধুরা সহর্ষে হুররে দিয়ে উঠল।
মণিমালা হেসে বলল, “হল কি তোমাদের? এত ফুর্তি?”
সিধু বলল, “বউদি, ওষুধ ধরেছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।”
ললিত বলল, “তোমার চাল টেরিফিক লেগে গেছে বউদি, এতটা আমরা ভাবিনি। তোমায় একটা মিনিস্ট্রি দেওয়া উচিত।”
মণিমালা উৎসাহিত হয়ে বসে পড়ে বলল, “শুনি শুনি, ব্যাপারটা বলো।”
সিধু বলল, “আর কোনো ব্যাপার নেই বউদি, আমি আসল গোয়েন্দা লাগিয়ে ছিলাম, বসন্ত বিলাপে রোজ দশ-পনেরোখানা করে আসছে।”
দত্তগুপ্ত বলল, “আরও আসবো গো বউদিদি; শ্যামচাঁদের পয়সায় রিপিট ডোজ্ আড়নের কথা ফাইন্যাল হইছে না।”
ললিত বলল, “হ্যাঁ ; আমরা ভাবছি—আর একবার—রোববারেই আর-একটা ঝেড়ে দিন ব্যাপারটা বেশ পোক্ত হবে। তুমি কি বল?”
শ্যাম বলল, “আপনার কনসেন্ট পেলেই আমরা দিয়ে দি।”
মাথা হেলিয়ে হেসে মণিমালা বলল, “বেশ ভাল কথাই তো। দিয়ে দিন।”
চার বন্ধুই আবার সহর্ষে চৌকি চাপড়াল।
শ্যাম বলল, “বউদি, আপনি সত্যিই গ্রেট।”
সিধু বলল, “আপনার কী মাথা! আমাদের ঘোল খাইয়ে দিতে পারেন।”
দত্তগুপ্ত বলল, “আপনারে অবশ্য আমাগো রসোগোল্লা খাওয়ান দরকার। …খাইবেন নাকি !”
হাসির চোটে ফেটে পড়তে পড়তে মণিমালা বলল, “মাঝপথে নয়, একেবারে শেষে। আগে আপনারা সত্যি সত্যিই জিতুন, তারপর।”
ললিত রঙ্গ করে বলল, “ফাইন্যাল ভিক্টরির পর তোমায় আমরা একমাস সিনেমা দেখাব, যে বই আসবে ; চপ কাটলেট মিঠে পান খাওয়াব, যত খেতে পার। যদি বলো তো আমাদের আড্ডার নামটাও তোমার নামে রেজিস্ট্রি করে দিতে পারি। …কিন্তু বউদি, মেয়ে বলেই তোমার এরকম প্যাঁচালো বুদ্ধি, ভীষণ অরিজিন্যাল কিন্তু সূক্ষ্ম। আমার ফিউচার যে কী, ভগবানই জানেন।”
মণিমালা হাসতে হাসতেই জবাব দিল। “তোমার বেলায় আরও সূক্ষ্ম হব।”
চার বন্ধুই হাসতে লাগল।
মণিমালা চলে গেলে ললিত তাস নিয়ে বসল।
শ্যাম নিজের হাতের তাস তুলে নিতে নিতে হঠাৎ বলল, “আচ্ছা ললিত, যদি বসন্ত বিলাপ হেরে গিয়ে আমাদের সঙ্গে ফায়সালা করতে চায়। ধর, কো-এক্সিটেন্স চায়। তা হলে?”
ললিত নিজের তাস গুছোতে গুছোতে জবাব দিল, “সেটা পরের ব্যাপার।”
“না, যদি চায় ; ধর না, ওরা চাইল। তা হলে?”
“তা হলে আমি ভাই আমার ফেভারিট—সেই ফ্লুরোসেন্ট মেয়েটাকে চাই—আলো চ্যাটার্জি।”
দত্তগুপ্ত বলল, “তোর চাওয়নে আলো জ্বলব কি সিধু?”
“আলবাত জ্বলবে। নয়ত কি তুই জ্বালাবি শালা?”
“আমার—” দত্তগুপ্ত বাঁ দিকের একটা তাস ডান দিকে টেনে নিল ; বলল, “আমার আলোয় কাম নাই, আমি ভূগোলরে বড়ই ভালবাসি রে সিধু, ভূগোলের ম্যাপখান দেখছস নাকি? আহা রে, চক্ষু সার্থক করে।” দত্তগুপ্ত যাকে ভূগোল বলল, তার নাম পার্বতী সেন, স্কুলের ভূগোল-দিদি।
ললিত অবশ্য তার অভিমত স্পষ্ট করে ব্যক্ত করল না, তবু বোঝা গেল তার পছন্দ কলেজের টীচার নবনীতাকে—যাকে ললিতরা বলে, কুলপি দিদি। এমনি নার্ভ? ঠাণ্ডা আঁটা সাঁটা দিদি।
শ্যাম তার অভিমত ব্যক্ত করল না।
দেখতে দেখতে আরও কিছুদিন কেটে গেল, দিন পনেরো, শ্রাবনের শেষাশেষি প্রবল বর্ষণ নামল। আকাশ যখন সঞ্চিত সব জল ঢেলে দিয়ে একটু ফাঁকা, ঈষৎ কৃপণ, মেঘলা ভাবটা আছে অথচ সারাক্ষণ বৃষ্টি নেই, ঝিপঝিপ করে জল আসছে, পালাচ্ছে, মাঝে মাঝে ইলশেগুঁড়ি ঝরছে তখন আবার এই ঘটনাটি ঘটল।
শ্যাম নিত্যকার মতন সন্ধেবেলায় ললিতের বাড়ি আড্ডা দিতে যাচ্ছিল। এখন আড্ডাটা আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে, কেননা সিধু রোজই প্রায় বসন্ত বিলাপের খবর আনছে। আগে যা ছিল বসন্ত বিলাপের অবস্থা এখন তার চেয়েও খারাপ। বসন্তের কুসুমগুলি এখন—এই সুন্দর বর্ষাতেও রীতিমত নির্জীব হয়ে পড়েছে। ক’দিন ধরে আর টু শব্দ শোনা যাচ্ছে না ওখানে, শ্যামদের আসাযাওয়ার পথে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে চার পাঁচজনে জটলা বাঁধিয়ে আর প্রচ্ছন্ন টিটকিরিও দিচ্ছে না। রাস্তাঘাটে চোখাচোখি হলে চোখ সরিয়ে নিচ্ছে। শ্যামরা সবাই খুশি। কতকগুলো মেয়ে পাড়ায় এসে জুড়ে বসে তাদের নাকাল করবে—এ হয় না। শত হলেও তোমরা মেয়ে। আস্কারা না দিলে তোমরা বাবা গাছে উঠতে পার? পার না।
বোনের ছাতা মাথায় তুলে শ্যাম আস্তে আস্তে হাঁটছিল। বিকেলের পর থেকে আবার ঝিপঝিপ বৃষ্টি চলছে। নেমেছিল জোরে, তবে প্রথম পশলাটা জোরে হবার পর ঝিপঝিপ করে চলছে। শ্যামের আজ মনটাও বেশ ভাল। তার হয়ত একটা প্রমোশন হতে পারে, অফিসে শুনছিল। ছোট প্রমোশন, তবু প্রমোশন তো।
ললিতদের বাড়ির রাস্তাটা আজ তিন-চার দিন ধরে অন্ধকারই পড়ে আছে। মিউনিসিপ্যালিটির আলো, জল ঝড় বৃষ্টিতে কোথায় কি গণ্ডগোল হওয়ায় তা আর এখনও সারানো হয়ে উঠল না। না উঠুক, চোখ বেঁধে দিলেও শ্যামরা এ-গলি দিয়ে চলে যেতে পারবে।
বেশ খানিকটা অন্ধকারের মধ্যে দিয়েই শ্যাম টিপটিপে বৃষ্টির মধ্যে হাঁটছিল। বসন্ত বিলাপের কাছে আসতেই শ্যাম তার সামান্য তফাতে কাকে যেন রাস্তায় উবু হয়ে পড়ে যেতে এবং ককিয়ে উঠতে শুনল।
উপেন স্যাকরার দোকান বন্ধ। হোমিও গিরিজার ডিসপেনসারিতে আলো জ্বলছে অবশ্য, কিন্তু সে আলো এতটা পৌঁছচ্ছে না। হোমিও গিরিজার আলোও হোমিও—একরত্তি, জ্বলে কি জ্বলে না বোঝা যায় না।
শ্যাম তাকাল। মাথায় কাপড় তোলা এক মহিলা। একেবারে রাস্তায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। পড়ে হাত পা চেপে যেন ককিয়ে ককিয়ে যন্ত্রণা প্রকাশ করছে।
বৃষ্টিটাও এ-সময় একটু বড় বড় ফোঁটায় পড়ছিল। মেয়েটি ছটফট করছে যন্ত্রণায়। নিশ্চয় অন্ধকারে আচমকা হোঁচট খেয়ে পড়েছে, কিংবা কোনো গর্তে পা দিয়ে ফেলেছে।
শ্যাম অবিবেচক হতে পারে না। পাড়ারই জানাশোনা কোনো বাড়ির বউ হবে।
এগিয়ে গিয়ে শ্যাম বলল, “কি হল, পড়ে গেলেন?”
যন্ত্রণা বোধহয় অতি তীব্র, অসহ্য ; মাথা নাড়িয়ে ছটফট করতে করতে আকারে প্রকারে এবং যন্ত্রণা-কাতর গলায় মেয়েটি যেন কি বলল ; শ্যামের মনে হল, ওকে তুলে ধরতে বলছে। পায়ে বোধ হয় জোর চোট পেয়েছে মেয়েটি।
শ্যাম উদ্বেগের গলায় বলল, “আপনাকে ধরব নাকি? উঠে দাঁড়াতে পারছেন না?”
মেয়েটি হাত বাড়িয়ে দিল সামান্য, শ্যামকে হাত ধরে উঠিয়ে দিতে বলছে।
শ্যামের এক হাতে ছাতা, অন্য হাত দিয়ে সে মেয়েটিকে সাহায্য করল উঠতে। বেচারি মেয়েটির গা হাত ভিজে, মাথার খোঁপা থেকে কাপড়টাও কাঁধে খসে পড়েছে। মুখ তুলতে পারছিল না যন্ত্রণায়, কান্নার গলায় বলল, “আমি সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছি না, ওপাশটায় একটু পৌছে দিন।”
শ্যাম হাত ধরে থাকল, সাহায্য করল আর মেয়েটি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে রাস্তার পাশে বাড়িটার চৌকাঠের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।
শ্যাম গোলমালে একেবারেই লক্ষ করেনি, মেয়েটি বসন্ত বিলাপের চৌকাঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। বরং শ্যাম জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, “গোড়ালি মচকে ফেলেছেন নাকি? কোথায় লেগেছে? একটা রিকশা ধরে দেব?” শ্যাম বুঝি মাত্র দু তিনটি শব্দ উচ্চারণ করেছে—হঠাৎ বুকের ওপর পিস্তল ধরে শাসাবার মতন করে সেই মেয়েটি শ্যামের পাঞ্জাবির বুকের কাছটায় ভীষণ জোরে মুঠো করে চেপে ধরে গর্জন করে বলল,“শিঘ্রি ভেতরে ঢুকুন, নয়ত চেঁচাব। ঢুকুন শিঘ্রি…।”
শ্যাম কিছু বোঝার আগেই মেয়েটি ঠেলে সদরের ওপারে ঢুকিয়ে দিল। আর শ্যাম দেখল দরজার পাশ থেকে সদরের গলি থেকে জনা চার পাঁচ মেয়ে বেরিয়ে এসে তাকে ঘিরে ফেলেছে।
একেবারেই বিমূঢ় বিহ্বল শ্যাম। তার পালাবার পথ নেই। ওই মেয়েটা যেটা রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে ককাচ্ছিল সে এখন দিব্যি সোজা পায়ে দাঁড়িয়ে দু চারবার যেন লাফও মারল, গলার স্বরে পিঁপড়ে কামড়াবারও কষ্ট নেই।
ভ্যাবাচাকা খেয়ে শ্যাম বলল, “মানে? আমায় এ-ভাবে—”
“মানে—?” সেই রাস্তার মেয়েটি বলল, “মানে বোঝাচ্ছি। এই লিলি, তোর হাতে কি আছে?”
“জিওমেট্রি বাক্সের কাঁটা।”
“ঠিক আছে। ও বেশি টেণ্ডাই মাণ্ডাই করলে প্যাঁক করে ফুটিয়ে দিবি।”
“মানে ব্যাপারটা কি, আপনারা……” শ্যাম কি স্বপ্ন দেখছে নাকি?
“শাট্ আপ্। কথা বললে ছুঁচ দিয়ে মুখ সেলাই করে দেব। এই অনিমা তোর হাতে কি আছে?”
“স্কেল।”
“শুভ্রা তোর কাছে কি আছে?”
‘কাঁচি।”
“আর কিছু বললেই ওর মাথার চুল কেটে দিবি ক্যাঁচ করে।”
শ্যাম আত্মরক্ষার জন্যে মাথার ছাতাটা গুটিয়ে ফেলল। একটা মাত্র দৌড়। পাঁচ পা দূরে চৌকাঠ, এদের ঝটকা মেরে ঠেলে ঠুলে পাঁচ পা এগুতে পারলেই শ্যাম বেঁচে যাবে। দেবে নাকি ধাক্কা? দু চারটে ঘুঁষি চালাবে? ছাতা পেটা করে পালাবে?
কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। কম্পাসের কাঁটা, স্কেল, রুল, কাঁচি—এবং না জানি আরও কি অস্ত্রশস্ত্র হাতে এই নারী বাহিনী তাকে ব্যুহ রচনা করে রয়েছে। শ্যাম পালাবার চেষ্টা করলেই এরা আক্রমণ করবে। সেই আক্রমণে শ্যামের ধুতি জামা, গায়ের চামড়া, মাথার চুল, পিতৃদত্ত নাক কান— থাকবে কি থাকবে না শ্যাম বুঝতে পারল না।
সেই মেয়েটা—যার পাকা অভিনয়ে ভুলে শ্যাম একেবারে বুন্ধুর মতন বসন্ত বিলাপে পা দিয়ে ফেলেছে, সে সঙ্গিনীদের বলল, “ওকে দোতলায় নিয়ে চল।” বলে শ্যামকে উদ্দেশ্য করে টিটকিরি মেরে হুকুম করল, “শুনুন শ্যামচন্দরবাবু, আপনাকে দোতলায় যেতে হবে। লক্ষ্মী ছেলের মতন চলুন। লিলি দরজাটা বন্ধ করে দে।”
শব্দ করে সদর বন্ধ হল। শব্দটা শ্যামের বুকের ওপর এমনই জোরে লাগল যে শ্যামের বুক ধকধক করতে লাগল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে শ্যামের, পা কাঁপছিল। শ্যাম ঠোঁট ভেজাচ্ছিল বার বার। ছি ছি, শ্যাম একটা মেয়ের চালাকির কাছে হেরে গেল। রাস্তার মধ্যে একবারও শ্যাম কেন মেয়েটার মুখ ভাল করে দেখল না, কেন বুঝল না—ওই মাথার কাপড় তুলে রাখার ব্যাপারটা পুরোপুরি ফল্স্, শ্যামকে ভাঁওতা মারা, এবং বৃষ্টির জল বাঁচানো। এখন শ্যাম মেয়েটাকে চিনতে পারছে, বিজয়া চৌধুরী, সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারে চাকরি করে।
শ্যামকে ওরা ঠেলছিল। শ্যাম বলল, “ব্যাপারটা কি হচ্ছে আমি বুঝতে পারছি না। কি করছেন আপনারা? দোতলায় আমি কেন যাব?”
শ্যামের কথায় সমস্বর একটা হাসি উঠল। বিজয়া বলল, “কেন যাবেন গিয়েই বুঝতে পারবেন।…কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, চলুন। আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর বৃষ্টিতে ভিজতে পারছি না।”
শ্যাম শেষবার প্রতিবাদ করে বলল, “যদি না যাই কি করবেন?”
“পুলিশ ডেকে আনব। বৃষ্টির মধ্যে সন্ধেবেলায় মেয়েদের হোস্টেলে ঢোকার জন্যে পুলিশে ধরিয়ে দেব।”
পুলিশের নামে শ্যামের সমস্ত পেটটা আমাশার ব্যথার মতন মোচড় দিতে লাগল। সর্বনাশ ! এরা সব ছকে রেখেছে যে!
অগত্যা শ্যাম এগুতে বাধ্য হল। বিজয়া শ্যামের আগে ; বাকি মেয়েরা শ্যামের পেছনে। সদ্য বন্দী শত্রুর মতন মেয়েরা শ্যামকে আগলে নিয়ে দোতলায় উঠে এল।
লিলি বলল, “প্রতিমাদির ডিউটি, আজ ফিরবে না। রাধাদি বলেছে—প্রতিমাদিদের ঘরেই নিয়ে যেতে।”
বিজয়া বলল, “রাধাদিকে ডাক। আর সবাইকে।”
শ্যামকে ঠেলে নিয়েই ওরা একেবারে শেষ প্রান্তের ঘরে ঢোকাল। ঘরে বাতি জ্বলছিল।
শ্যাম ঘরটা একবার দেখল : গোটা তিনেক তক্তপোশ, বিছানা পাতা ; কাঠের আলনা, দড়ির আলনা, শাড়ি সায়া জামা ঝুলছে; কাঠের সস্তা র্যাক আর টেবিল—বইপত্র, কাগজ মাথার তেল, ক্রীম পাউডার, চুলের ফিতে, ওষুধের শিশি আরও কত কি।
শ্যামকে কেউ বসতে বলল না। বেচারি দাঁড়িয়ে থাকল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আলোতে সে তার শত্রুপক্ষকে দেখতে লাগল। সব কটার মুখে চাপা হাসি, বিজয় গর্বের হাসি তো বটেই, তার সঙ্গে বাঁকা হাসিও মেশানো। প্রচ্ছন্ন একটা কৌশলের আভাসও যেন ওদের চোখে মুখে ফুটে আছে।
লিলি খোঁচা মেরে বলল, “তোয়ালে এনে দেবে নাকি? গা-মাথা মুছবেন?”
শ্যাম মাথা নাড়ল, না।
অনিমা বলল, “একটা ময়লা গামছা এনে দে বরং, ওই মাথা আর তোয়ালে দিয়ে মোছে না।”
আবার এক দফা হাসি উঠল। শ্যাম দেখল, নিচে থেকে তাকে যারা ধরে এনেছিল দোতলায় এসে তাদের দল আরও ভারি হয়ে উঠেছে। আলো চ্যাটার্জী, পার্বতী সেন, মীনা গুপ্ত—সবাই আছে। শ্যামের কান্না পাচ্ছিল।
এমন সময় পায়ে শব্দ তুলে এবং গলায় আওয়াজ দিয়ে সিংহবাহিনী—অর্থাৎ সেই অনুরাধা সিংহ এল। মেয়েরা সবাই গা সরিয়ে তাদের রাধাদি—অর্থাৎ, বাহিনীর সবাধিনায়িকার জায়গা করে দিল। রাধার হাতে একটা ফাইল, আর চোখে চশমা।
নাক কোঁচকালো, ঠোঁট ওলটালো তারপর অনুরাধা ঘরে ঢুকে শ্যামকে একবার আপাদমস্তক তির্যক চোখে, সঘৃণায় লক্ষ করল, এগিয়ে গিয়ে জানলার দিকে দাঁড়াল। শ্যামের পা তখন রীতিমত থরথর করে কাঁপছে, গলার কাছে সোডার গুলির মতন ভয়ের একটা শক্ত বল আটকে আছে। শ্যামের মনে হল সে একেবারে অনুরাধার পায়ের ওপর পড়ে পা জড়িয়ে ধরে।
একটা চেয়ার টেনে অনুরাধা—বা রাধা বসল। বসেই হুকুম করল, “ওকে একটা টুল দে বসার।”
কে যেন একটা টুল এনে দিল।
রাধা গম্ভীর গলায় বলল, “দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলির পাঁঠার মতন কাঁপতে হবে না। ওই টুলে বসা হোক।”
দাঁড়িয়ে থাকার অবস্থা শ্যামের ছিল না। সে সত্যিই বলির পাঁঠা। শ্যাম নিজেকেও নিজে পাঁঠা বলল। এবং অসহায়ের মতন বসল।
শ্যামকে আবার ভাল করে দেখে রাধা বলল, “মাথাটাথা মোছা হবে নাকি?”
মাথা নাড়ল শ্যাম। না।
“ভাল। ……তা মশায়ের নাম কি শ্যামচন্দ্র?”
“না, শুধু শ্যাম।”
“শ্যামের পর কিছু নেই?”
“না” শ্যাম বলল, বলেই সে এত বিপদের মধ্যে একটা বিদ্বেষপূর্ণ রসিকতা করে বলল, “শ্যামের পাশে মানাবার মতন কিছু এখনও খুঁজে পাইনি।”
রাধা ইঙ্গিতটা বুঝল। মেয়েরাও ঠোঁটের ফাঁকে হেসে ফেলেছে। খানিকটা যেন ব্যঙ্গ করেই রাধা বলল, “টিকটিকির আবার পাখা গজাবার সাধ !…তা কেষ্ট ঠাকুরের বাবার নাম কি অনাদিচরণ বাবু?”
“আজ্ঞে হ্যাঁ।”
“পলাশ পাড়ার দিকে থাকা হয়?
“হ্যাঁ।”
“বয়স কত?”
“চৌত্রিশ।”
“চাকরি বাকরি তো মোটামুটি ভালই করা হয়।”
“চাকরি একটা করা হয়।”
রাধা এবার মুহূর্ত কয় চুপ করে থেকে সঙ্গিনীদের দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে যেন কি কথা বলে নিল। পরে বলল, শ্যামকেই, “সেদিন স্টেশনে আমার কাপড় পুড়িয়ে ছিল কে?”
শ্যাম এভাবে চোরা মার খাওয়া বরদাস্ত করতে পারছিল না। বলল, “আমি সেদিন ইচ্ছে করে আপনার শাড়ি পোড়াইনি। অ্যাকসিডেন্টলি হয়ে গেছে। আমার অবশ্য কেয়ারফুল হওয়া উচিত ছিল। আমি তার জন্যে ক্ষমা চেয়েছি।…যদি তাতেও না হয়ে থাকে, শাড়ির দাম দিতে রাজি।”
আলো টিটকিরি দিয়ে বলল, “ইস্…খুব যে টাকার তেজ।”
পার্বতী বলল, “তেজস্ক্রিয় না কি বলে যেন, একেবারে তাই, না রে আলো!”
খিল খিল হাসি উঠল মেয়েদের মধ্যে।
শ্যামের আর সহ্য হচ্ছিল না। কান, নাক, চোখ জ্বালা করছিল। শ্যাম রাধার দিকে তাকিয়ে বলল, “আমায় এখানে এভাবে কেন ধরে আনা হয়েছে আমি জানতে চাই।”
লিলি একটা মন্তব্য করল : আহা রে, কচি খোকা…।
রাধা বলল, “কেন ধরে আনা হয়েছে আপনি জানেন না?”
“না। এটা অন্যায়।”
রাধা যেন সাঁড়াশির মতন চোখ করে শ্যামের দিকে তাকিয়ে বলল, “আপনাকে কি জামাই আদর করার জন্যে ধরে আনা হয়েছে ভাবছেন?”
“না, তা তো নয়ই। দেখতেই পাচ্ছি।” বলে শ্যাম কাঁটা, কম্পাস, স্কেল, কাঁচি সজ্জিত মেয়েদের দিকে তাকাল।
রাধা বলল, “এ বাঁদরামি কে করেছে?”
“কি ?”
“জানেন না। …এই লিলি দে তো তোর হাতের কাঁটা দুটো। দেখছি জানে কি না।” বলে রাধা হাতের ফাইলটা নাড়ল। “বলি, কাগজে—বাংলা কাগজে—কে আমাদের ঠিকানা দিয়ে বিয়ের বিজ্ঞাপন ছেপেছে?”
শ্যাম একেবারেই চুপসোনো ফানুসের মতন হয়ে গেল। তার অবশ্য মনে মনে এরকম একটা সন্দেহ হচ্ছিল, কিন্তু ব্যাপারটা এত গোপনে করা হয়েছে যে বসন্ত বিলাপের মেয়েদের জানার কথা নয়। কোথায় কলকাতায় কাগজে টাকা পাঠিয়ে বিজ্ঞাপন ছাপার ব্যবস্থা আর কোথায় এরা? কি করে জানবে?
রাধা ততক্ষণে আবার জোরে ধমকে উঠেছে। “কে দিয়েছে বিজ্ঞাপন?”
শ্যাম আত্মরক্ষার জন্যে দিশেহারা হয়ে গেল। সর্বনাশ, তাদের কীর্তি যে ফাঁস হয়ে যাচ্ছে! ব্যাপারটা শাড়ি পোড়ানোর চেয়ে মারাত্মক, শ্যাম যদি স্বীকার করে নেয় তবে এই বসন্ত বিলাপের দল তার ছালচামড়া ছিঁড়ে নিয়ে ডুগডুগি বাজাতে বসবে।
চুপসোনো মুখে, গোঁ গোঁ শব্দ করতে করতে শ্যাম খানিকটা থুধুই গিলে ফেলল। অসহায়ভাবে মাথা নেড়ে বলল, “আজ্ঞে আমি কিছু জানি না। কিসের বিজ্ঞাপন?”
রাধা চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল। “জানেন না?…মিথ্যেবাদী, লায়ার চোর…।”
শ্যাম প্রায় হাতজোড় করে বলল, “সত্যি বলছি, বিশ্বাস করুন।”
“এই আলো—” রাধা রক্তচক্ষু হয়ে হাত বাড়ালো, “ওই পাখাটা দে তো, আজ আমি ওর মাথায় পাখার বাঁট ভাঙব।”
আলো একটা বিছানার পাশ থেকে একটা পাখা তুলে নিল।
শ্যাম বলল, “আপনারা সবাই মিলে আমার ওপর অত্যাচার করছেন।” বলার সময় দেখল পাখাটা সিংহবাহিনীর হাতের কাছে নিয়ে আলো দাঁড়িয়ে আছে।
“কাগজে বিয়ের বিজ্ঞাপন আপনারা দেননি?” রাধা ধমকে ধমকেই বলল, “আমাদের বাড়ির ঠিকানা দিয়ে পাত্র চাই বলে কে তাহলে বিজ্ঞাপন দিয়েছে?”
শ্যাম গোবেচারি ও ন্যাকা-বোকার মতন করে বলল, “আমি কি করে জানব। কিসের বিজ্ঞাপন ?”
রাধা হাতের ছোট ফাইল খুলে কিছু কাগজপত্র সরিয়ে, দুটো কাগজ বের করল। শ্যামের কাছে এগিয়ে এসে ভাঁজ করা কাগজের একটা জায়গা দেখাল, লাল পেনসিলের ঘেরা দেওয়া। শ্যাম দেখার ভান করল।
“এই বিজ্ঞাপন কে দিয়েছে?” রাধা জেরা শুরু করল।
“আমি জানি না।”
“মিথ্যুক, বেয়াদব। …..এই বিজ্ঞাপনে কি লেখা হয়েছে জানেন না আপনি?”
“কি করে জানব?”
“লেখা হয়েছে যে এই ঠিকানায় বামুন, কায়স্থ, বদ্যি উজ্জ্বল শ্যাম, শ্যাম, গৌরাঙ্গী, বয়স্ক, কম বয়স্কা চাকরি করা বহু পাত্ৰী আছে। বিবাহযোগ্যা এই মেয়েদের জন্যে পাত্র চাই।”
শ্যাম পর পর দুবার ঢোঁক গিলল।
“বিজ্ঞাপনটা ক’বার বেরিয়েছে জানেন?”
“আজ্ঞে না।”
“দু বার। দ্বিতীয়বার আরও নতুন নতুন কথা আছে।”
‘ও !”
“কত চিঠি এসেছে জানেন—এই ঠিকানায়?…কত চিঠি এসেছে অনিমা?”
“অনেক—প্রায় দুশো তো হবেই। এখনও আসছে।”
“তাহলে?” রাধা শ্যামের দিকে ছুরির মতন ধারালো চোখে তাকাল। “কি বলার আছে আপনার?”
বলার বাস্তবিকই কিছু নেই। ভেজা মাথায় বসে থাকতে থাকতে শ্যাম হাঁচল।
বিজয়া লিলির হাত থেকে জ্যামিতি বাক্সর দুমুখো ছুঁচলো কাঁটা কেড়ে নিয়ে এসে শ্যামের একেবারে হাতের কাছে দাঁড়াল, দাঁড়িয়ে কাঁটাটা শ্যামের মুখের কাছে তুলে বলল, “ক্যাবলার মতন করে তাকাবেন না, চোখে ফুটিয়ে দেব প্যাঁক করে।”
শ্যাম ভয়ে চোখের পাতা বুজে ফেলল।
আলো বলল, “অত দরকার কি, পুলিশে দিয়ে দে না! পুলিশের জিম্মায় দিয়ে দে। আর সঙ্গে সঙ্গে সম্ভ্রমহানির একটা মামলা সবাই মিলে ঠুকে দি। দেখি ধর্মের ষাঁড় কোথায় পালায়?”
শ্যাম ভয়ে আঁতকে উঠে বলল, “মামলা?”
“বাঃ, মামলা করব না—” আলো বলল, “আমাদের মান সম্মান সম্ভ্রম, আমাদের পারিবারিক সুনাম নষ্ট করে যারা আমাদের সম্মানহানি করছে তাদের নামে মামলা করব না!…এতগুলো মেয়ের একসঙ্গে মামলা দেখি, কোর্ট কি করে ছাড়ে আপনাদের।”
শ্যাম আর কোথাও কোনো পথ দেখতে পেল না। শালা শেষপর্যন্ত। মেয়েছেলেদের ব্যাপার নিয়ে মামলা? ক্রিমিন্যাল কেস হবে নাকি? হতে পারে। বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে, সারা শহরে রই রই পড়ে যাবে, জেলে গিয়ে ঘানি ঘোরাতে হবে। শ্যাম যেন ঘামতে লাগল। “আপনারা আমায় একলা পেয়ে যা খুশি বলছেন।”
ভিড়ের মধ্যে থেকে কলেজের টীচার নবনীতা এগিয়ে এসে বলল, “রাধা, উনি যদি এ-সময় কাউকে ডাকতে চান ডাকতে পারেন। ওঁদের তরফে যদি কিছু বলার থাকে শুনে নেওয়া যাক।”
রাধা বলল, “বেশ। একজনকে ডাকতে পারেন। যে কোনো একজনকে।”
“কি করে ডাকব! আমি এখানে?”
“দু’লাইন লিখে দিন, আমরা আনিয়ে নিচ্ছি। …ওবাড়িতে আড্ডায় নিশ্চয় পাব।”
লিলি সঙ্গে সঙ্গে কাগজ কলম এনে দিল। রাধা বলল, “কোনো আজে বাজে কথা লেখা চলবে না। কোথায় আছেন তাও নয়। শুধু লিখবেন—বিশেষ জরুরী, একবার আসতে। লেখাটা আমরা দেখে নেব।”
শ্যাম সামান্য ভাবল। কাকে এ-সময় আসতে লেখা যায়? সিধুকেই লেখা যাক। সিধু নিশ্চয় এসে বসে আছে আড্ডায়। সিধুটা একটু গুণ্ডা গোছের। দত্তগুপ্ত কিছু করতে পারবে না। ললিতটা আরও নার্ভাস। শ্যাম লিখল: “সিধু, পত্রপাঠ চলে আসবি। ভীষণ বিপদ।”
লেখাটা রাধা পড়ে দেখল, তারপর বিজয়াকে দিয়ে বলল, “যা, আর-একটাকে ধরে আন। ওবাড়িতে কেউ যাবি না তোরা, নিচে থাকবি। ঝিয়ের ছেলেটাকে পাঠিয়ে দে। বলে দিস কিছু না বলে যেন।”
বিজয়ারা একদল দৌড়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল।
ঘরে শ্যাম টুলে বসে। আর ওদিকে রাধা, চেয়ারে ফিরে এসে বসেছে। নবনীতা বিছানায় বসে আস্তে আস্তে পায়ের পাতা কাঁপাচ্ছিল: আলো দরজার দিকে একটা টেবিলের কোণায় আধ-বসা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
প্রায় চুপচাপ। শ্যাম আটক-করা চোরের মতন হতাশ হতোদ্দম হয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। ঘরের জানলায় মোটা শিক, রাস্তার বারান্দার দিকের দরজাটা বন্ধ, ঝিপঝিপে বৃষ্টি পড়েই চলেছে। শ্যাম যে বারান্দা থেকে নিচে রাস্তায় লাফ মারবে তার সাহস নেই, উপায়ও নেই। দৌড় মেরে নিচে পালানোও অনর্থক, নিচে পুরো ফৌজ দাঁড়িয়ে আছে সিধুকে ধরে আনার জন্যে। অগত্যা শ্যাম ঘরের জিনিসপত্র, বিছানা, শাড়ি জামা, এটা-সেটা লক্ষ করতে লাগল। করতে করতে সে দেখল, কোণার দিকে দড়ির আলনায় বেশ বাহারী একটা ব্রেসিয়ার ঝুলছে। এই ঘরে কে কে থাকে শ্যাম জানে না; প্রতিমাদি থাকে শুনেছে; আর কে? শ্যাম আড়চোখে ব্রেসিয়ার দেখতে লাগল এবং নানা রকম অনুমান করছিল।
সিধু শালা আসবে তো? নাকি ব্যাপারটা আঁচ করতে পেরে এ-পথ আর মাড়াবে না? বন্ধুর বিপদে সিধু যদি না আসে তবে শ্যাম তার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখবে না। সিধু, ললিত, দত্তগুপ্ত—সকলেরই এখানে এসে দেখে যাওয়া উচিত শ্যাম কেমন করে কাদায় ডুবে গেছে। একা শ্যাম কেন—ওই তিনটেরও একই হাল হওয়া দরকার, শ্যাম একা জেলে যেতে পারবে না। মণিমালা বউদির কথায় খুব নেচে ছিল সবাই। এবার ঠেলা সামলাও। বউদির ওপর শ্যামের রাগ হচ্ছিল, স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী।
শ্যাম আবার হাঁচল, একসঙ্গে বার পাঁচেক।
রাধা ভুরু কুঁচকে ধমকে উঠে বলল, “হাঁচির হাট বসিয়ে দিচ্ছেন যে! হাঁচিতে রোগ ছড়ায় সে জ্ঞান নেই। হাঁদা কোথাকার!”
শ্যাম তাড়াতাড়ি নাকে মুখে রুমাল চাপা দিল।
নবনীতা রসিকতা করে বলল, “শ্যামবাবুর জন্যে একটু আদা-চা এনে দে, আলো।”
আলো গা দুলিয়ে ঘাড় হেলিয়ে বলল, “চা খাবেন নাকি শ্যামবাবু?”
মাথা নাড়ল শ্যাম; না খাবে না। আলো—সিধুর ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প—সত্যিই বেশ জ্বলজ্বলে। বড় বড় চোখ, ডাসা নাক, বেশ স্লিপ্মারা চেহারা।
নবনীতা আর রাধা নিজেদের মধ্যে কথা বলছে যদিও তবু শ্যাম বুঝতে পারছে—কথাটা শ্যামদের নিয়ে, পুলিশ ডাকা মামলা করা এইসব সংক্রান্ত। শ্যামের মাথা ধরে উঠছিল।
এমন সময় নিচের দিকে হইহই। সিঁড়িতে দুপদাপ। তারপর সিধুর গলা।
সিধুকে চারপাশ থেকে ঘিরে মেয়েরা ঘরে ঢুকল। সিধুর অবস্থা ভাল নয়, একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে, মাথার চুল এলোমেলো, জামার একটা পকেট ছিঁড়ে গেছে, সিধু জড়সড়, কাঠ।
সিধু ঢুকতেই শ্যাম প্রায় ছেলেমানুষের মতন ডুকরে উঠল, “সিধু!”
সিধু সিংহবাহিনীর মুখোমুখি হয়ে একেবারে ভূত দেখার মতন আঁতকে উঠল। তার গলায় আর শব্দ বেরোচ্ছে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিধু কিম্ভূত ধরনের একটা শব্দ করল।
রাধা মেয়েদের বলল, “আর একটা টুল-ফুল এনে দে ওকে। ভিরমি খেয়ে না পড়ে যায়!”
শ্যাম আবার ডাকল, “সিধু।”
ধাতস্থ হতে সিধুর একটু সময় লাগল। কিন্তু ধাতস্থ হবার পর সিধু বেশ তাড়াতাড়ি সাহস সংগ্রহ করতে লাগল। একটা ভাঙা মোড়া এনে দেওয়া হয়েছিল সিধুকে বসতে। সিধু শ্যামের পাশে বসল।
রাধা বলল, “নামটা কি সিদ্ধেশ্বর গাঙ্গুলী?”
সিধু মাথা হেলিয়ে সায় দিল। বলল, “আমাকে এখানে আনার মানেটা কি?” বলে শ্যামের দিকে তাকাল। “কি হয়েছে রে?”
শ্যাম অসহায়ের মতন বলল, “আমাকে এঁরা রাস্তা থেকে ধরে এনেছেন।”
“ধরে এনেছে!…কচি খোকা!” আলো টিটকিরি মেরে মন্তব্য করল।
সিধু আলোর দিকে তাকাল। “শ্যাম নিজে এখানে আসতেই পারে না।”
লিলি বলল, “আসবে কি করে? এলে যে পা খোঁড়া করে দেব।”
রাধা বলল, “চুপ! তোরা চুপ করে থাক।”
মেয়েরা চুপ করে গেল।
রাধা সিধুকে বলল, বেশ গম্ভীর পরিষ্কার গলায়, “আপনার বন্ধুকে আমরা রাস্তা থেকে ধরে এনেছি। হ্যাঁ—এনেছি।”
“এটা কিডন্যাপিং…”
নবনীতা হাসল। বলল, “কেন এনেছি জানেন?”
“না।”
রাধা বলল, “আপনারা ইতর, অসভ্য, জন্তু…।”
সিধু চোখ বড় বড় করে চেয়ে থাকল।
রাধা বলল, “ধরে আনার কারণ আপনার পেয়ারের বন্ধু শ্যামচন্দরকে বলা হয়েছে শুনে নিন।”
সিধু শ্যামের দিকে তাকাল। অবশ্য সিধু এতোক্ষণে সবটাই বুঝতে পেরেছে।
শ্যাম বলল, “খবরের কাগজে—রবিবারের কাগজে—একটা বিয়ের বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে ভাই। এখানকার, এ বাড়ির ঠিকনা দিয়ে। তাতে নাকি লেখা আছে—এখানে নানারকম—ভেরিয়াস টাইপের মেয়ে পাত্রী আছে, বিয়ের যুগ্যি। …সেই বিজ্ঞাপন বেরুবার পর চিঠি এসেছে অনেক…”
বাধা দিয়ে একজন কে বলল, “ঘটকও এসেছে।”
শ্যাম নিজের কথা শেষ করল। “এঁরা বলছেন বিজ্ঞাপনটা আমরা দিয়ে দিয়েছি। দেখ তো ভাই, কী রকম খারাপ অ্যালিগেশান।”
সিধু হঠাৎ বলল, “মাইরি আর কি!”
সঙ্গে সঙ্গে আলো জিভ ভেঙিয়ে বলল, “আহা, ইললি রে…”
রাধা চেয়ারে বসে সিধুকে ধমকে উঠল জোরে, “ছোটলোকের আড্ডা নাকি এটা? মাইরি-ফাইরি চলবে না। ভদ্র ভাষায় কথা বলুন।”
সিধু বলল, “ইললি বললে দোষ নেই?”
“বাজে কথা থাক। কাজের কথার জবাব দিন।”
“বলুন।’
“বিজ্ঞাপনটা আপনারা দিয়েছেন।”
“আপনারাও দিতে পারেন।”
আলো ছুটে এল, যেন সিধুর মাথার চুলের ঝুঁটি ধরেই নেড়ে দেবে। বলল, “আমরা বিজ্ঞাপন দিয়েছি। মিথ্যেবাদী, পাজি…”
সিধু বলল, “আমরাই বা দেব কেন? বিজ্ঞাপন দিতে পয়সা লাগে। আপনাদের জন্যে আমরা চ্যারিটি করব কেন?”
একটু চুপ। নবনীতা মৃদু হেসে বলল। “তা ঠিক। তবে এখানে সেটা করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনের টাকা আপনারা দিয়েছেন।”
সিধু এবার সন্দিগ্ধ হল। “বাজে কথা, মিথ্যে কথা। আমাদের এতে স্বার্থ কি?”
আলো বলল, “ষোলো আনা স্বার্থ।”
সিধু বলল, “এক আনাও নয়।”
রাধা বলল, “বেশ। কিন্তু সিধুবাবু, গোঁসাই-মশাই, যদি আমরা দেখাই যে এই বিজ্ঞাপন আপনারা দিয়েছেন, তা হলে?”
সিধু ভেতরে ভেতরে ভয় পেলেও মুখে প্রকাশ করল না। বলল, “প্রমাণ থাকলে অন্য কথা।”
“থাকলে কি হবে আগে বলুন?”
“কি আর—” সিধু ঘাবড়ে গেল, “আমাদের যা খুশি করবেন আপনারা।”
“আমরা প্রথমে পুলিশে যাব। শ্যামচন্দরকে আজই হাজতে ঢোকাব। আর আপনাদের নামে মামলা করব। আমাদের এতগুলো মেয়ের সামাজিক ও পারিবারিক মান সম্মান সম্ভ্রম নষ্ট করার জন্যে। বুঝলেন?”
সিধু সবই বুঝতে পেরে গেছে এতোক্ষণে, শ্যামের দিকে ঘাবড়ানো-চোখে চাইল। নিচু গলায় বলল, ‘আলোর সুই কোথায় রে?’…শ্যাম ফিসফিস করে বলল, “কোন্ আলো?”
রাধা চিৎকার করে বলল, “কানে কানে কথা বলার কিছু নেই। আমরা যা বললাম তাই করব।”
সিধু কাষ্ঠ-হাসি হেসে বলল, “আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনারা যা ভাল বোঝেন করবেন। কিন্তু প্রমাণটা… ?”
রাধা তার হাতের ছোট ফাইল ওলটালো। বলল, “আমরা কলকাতার কাগজের অফিস থেকে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, এখান থেকে মানি অর্ডারে টাকা পাঠানো হয়েছে শ্যামচন্দরের নামে। কলকাতায় আমাদের লোক আছে। কবে কত টাকা পাঠানো হয়েছে তাও বলতে পারি। এগারোই জুন আর পয়লা জুলাই। কাগজের অফিসে আমরা চিঠি লিখেছিলাম, তার জবাবও এখানে আছে—দেখতে চান?”
শ্যাম টুল সমেত মাটিতে হাঁটু গেড়ে পড়ল। সিধু একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে হাত জোড় করে কি বলতে গেল। কেউ কোনো কথা শুনল না। আলো সিধুকে চিমটি কাটল বেজায় জোরে, লিলি সিধুর ছেঁড়া পকেট ধরে টান মেরে বাকিটাও ছিঁড়ে দিল। অনিমা শ্যামের পিঠে গুম্ মেরে এক কিল বসিয়ে দিল, আর পার্বতী কুঁজোর জল শামের মাথায় ঢেলে দিল। ওরই মধ্যে কে যেন সিধু এবং শ্যামকে সেফটিপিন দিয়ে ফোটাল, জ্যামিতি বাক্সের দু-মুখো কাঁটা দিয়ে খুঁচিয়ে দিল, দু-চারবার স্কেলের বাড়ি পড়ল।
শ্যাম এবং সিধু পাশাপাশি মাটিতে বসে জোড় হাতে ক্ষমা ভিক্ষা করতে করতে বলল, “আর না, প্লিজ, মরে যাব।”
রাধা হুকুম করল কড়া গলায়। “এই ওদের ছেড়ে দে।”
মেয়েরা সরে দাঁড়াল।
রাধা বলল, দোষ স্বীকার করছেন?”
শ্যাম বলল, “আজ্ঞে হ্যাঁ, করছি। …আপনার পায়ে পড়ছি…”
সিধু বলল, “আমাদের মাপ করুন।”
রাধা বলল, “কিন্তু এই যে আমাদের ইজ্জত নষ্ট করা হয়েছে, এর কি হবে?”
শ্যাম বলল, “যা বলবেন তাতেই রাজি। আমাকে প্লিজ পুলিশে দেবেন না। পুলিশের নাম শুনলেই আমার ডিসেন্ট্রি হয়। মামলা যদি করেন—সে স্ক্যাণ্ডেলাস হবে। শহরে টিকতে পারব না। বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেবে। চাকরি যাবে।”
নবনীতা বলল, “এ জ্ঞান আগে হয়নি?”
সিধু বলল, “আজ্ঞে না, হলে কি এ-পথ মাড়াই।”
রাধা বলল, “অত সস্তায় চিঁড়ে ভেজে না। এই অপমান, দুর্নাম, সম্ভ্রমহানির ক্ষতিপূরণ কে দেবে?”
শ্যাম এবং সিধু মুখ চাওয়াচাওয়ি করল।
শ্যাম বলল, “আজ্ঞে, আমাদের কি আছে বলুন—?”
সিধু বলল, “যৎসামান্য মানুষ আমরা, ক্ষতিপূরণ কি করেই বা দিতে পারি?”
রাধা বলল, “তা হয় না। শুধু হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় না।”
“মুচলেকা দিচ্ছি।” সিধু বলল।
এমন সময় ঘরের মধ্যে হাসির অট্টরোল পড়ে গেল। মেয়েদের ভিড় সরিয়ে মণিমালা কোথা থেকে এসে হাজির। পেছনে হন্তদন্ত ললিত আর দত্তগুপ্ত।
রাধা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে একেবারে অন্য মূর্তি হয়ে গেল। হেসে, গড়িয়ে আহ্লাদে আটখানা হয়ে বলল, “একেবারে কাঁটায় কাঁটায় এসে পড়েছে, মণিদি, ব্যাঙ কুয়োয় পড়েছে।”
মণিমালা হাসি চাপতে পারছিল না। মুখে আঁচল চাপা দিয়ে বলল, “এ কি করেছিস রে ওদের? ওমা ছি ছি! আপনারা ভাই উঠে বসুন।”
শ্যাম সিধুর দিকে তাকাল, সিধু শ্যামের দিকে, তারপর দুজনেই ললিত ও দত্তগুপ্তর দিকে তাকাল। ললিতরাও কিছু কম হতবাক নয়। সিধু মণিমালার দিকে তাকিয়ে শেষে বলল, “বউদি, এটা খুব আনফেয়ার কাজ হল। আপনি ট্রেচারি করলেন আমাদের সঙ্গে।”
শ্যাম বলল, “কনস্পিরেসি।”
ললিত ক্ষুব্ধ গলায় বলল, “তুমি আমাদের গাছে চড়িয়ে মই কেড়ে নিলে বউদি, এখন বুঝতে পারছি তোমার চালটা কাদের তরফের ছিল।”
দত্তগুপ্ত বলল, “আমাগো খুব খেলাইলেন, বউদিদি। আপ্নারে দণ্ডবৎ।”
মেয়ের দল অট্টহাসি হেসে উঠল। নানা গলার, নানা সুরের হাসি। হাসির চোটে ঘরটা ফেটে যাবার জোগাড়।
মণিমালার নাকে-চোখে জল এসে গেছে হাসতে হাসতে। নাক-চোখ মুছে হাসি সামলে বলল, “কেন ভাই, দোষটা কি করলাম। আপনাদের কত হা-হুতাশ ছিল। আমি বরং বসন্ত বিলাপের ঘরে এনে বসিয়ে দিলাম এরপর যার যেমন, কপাল…”
আলো বলল, “কপাল কেন বলছেন মণিদি, বলুন কেরামতি। কার কত কেরামতি।”
সিধু আলোর দিকে তাকাল। তারা উঠে দাঁড়িয়েছে। সিধু দেখল, আলোর সুইচটা হাতের কাছেই। কেরামতি করতে অবশ্য সাহস করল না।
ললিত একপলক নবনীতার দিকে তাকাল। তাকিয়ে কী রকম লজ্জা পেল।
দত্তগুপ্ত ঝট্ করে ভূগোলদিদি পার্বতীকে চোখ টিপে দিয়েই গম্ভীর হয়ে গেল।
মণিমালা বলল, “রাধা এদের তাহলে…”।
রাধা বলল, “এখনকার মতন থাক। তবে ক্ষতিপূরণ তো দিতেই হবে। পরে দেবে। আমরাও ভেবে দেখি।”
সিধু বলল, “তেমন তেমন হলে দিতে পারি। মুচলেকাও।”
শ্যাম বলল, “ওয়ার্ড অফ অনার বউদি। …আমরা এবার যাই?”
“যান।” রাধা সম্মতি দিল।
যাবার সময় মেয়েরা রসিকতা করে একটু উলু দিয়ে নিল।
মাস খানেক হয়নি, ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টির মধ্যে সন্ধেবেলায় শ্যাম আর রাধা একই সঙ্গে একটা রিকশা করে স্টেশন থেকে ফিরছিল।
রেল অফিসের সামনে জোড়া কদম গাছের তলায় এসে শ্যাম বলল, “তোমার পদবিটা বড় ফেরোশাস রাধা, সিংহী। ওটা বদলে নিলে কেমন হয়?”
রাধা শ্যামের কাঁধের কাছে আলগা ঠেলা দিয়ে বলল, “বদলে নিলেও কি তোমার লাভ হবে কিছু, আমি সিংহীর মতনই থাকব।”
“তা থাকো। তাতে আমার আপত্তি নেই।”
“নেই?”
“না, আপত্তি কিসের! আমি তো তোমার খাঁচায় ঢুকে পড়েছি।…তবে পদবিটা পালটে নাও!…আ, ফার্স্ট ক্লাস কদমফুলের গন্ধ দিয়েছে।”
রাধা বলল, “শুধুই কি গন্ধ! কদমতলায় একেবারে শ্যাম রয়েছেন যে!”
“রাধাও।” শ্যাম হেসে বলল। দু’-জনেই ঘন হয়ে হাসতে লাগল হঠাৎ।
বিউটি এবং জিজি
গোবিন্দ চেম্বারে আসতেই রোগীরা থ’ হয়ে গেল। আগেই সমস্বরে আর্তনাদ করার কথা কিন্তু রাস্তা দিয়ে সাইকেল ঠেলে আসার সময় কেউ বুঝতেই পারেনি কাদায় গোবরে মাখামাখি, সুরকির লাল প্রলেপে রঞ্জিত হয়ে যে আসছে সে-ই গোবিন্দ ডাক্তার।
রোগীরা হুঁশ ফিরে পেয়ে ‘কি হল—কি হল’ করার আগেই গোবিন্দ রোগীদের বসার ঘর দিয়ে ভেতরে চলে গেল। কাদা, গোবর, সুরকির গন্ধ যেন ঘরের মধ্যে ঘিন ঘিন করতে লাগল কিছুক্ষণ, পাখার বাতাসে সেটা ক্রমশ উবে যেতে লাগল। চাটুজ্যেবাবু বললেন, “নিশ্চয় ষাঁড়ে গুঁতিয়েছে। বাজারের ওই ষাঁড়টা একটা ন্যুইসেন্স হয়ে গেল। মিউনিসিপ্যালিটি ষাঁড়টাকে কিস্যু করছে না।”
অনন্ত পেটের ব্যথায় ছটফট করছিল, বলল, “পাগলা কুকুরে তাড়াও করতে পারে। একটা পাগলা কুকুর বেরিয়েছে রাস্তায়।”
বাইরের ঘরে রোগীরা হরেক রকম আলোচনায় যখন মত্ত ভেতরে ততক্ষণে অন্য কাণ্ড হচ্ছে। ভেতরে খানদুয়েক ঘর, ছোট ছোট। একটা বাথরুম। দুটো ঘরের একটাতে গোবিন্দর কম্পাউন্ডার ওষুধপত্র তৈরি করে, অন্যটায় হাবিজাবি পড়ে থাকে, চা তৈরি হয়, মেয়ে রোগীদের জন্যে একটা সরু টেবিলও পড়ে আছে। গোবিন্দর কম্পাউন্ডারের নাম তারক। বয়েস এমন কিছু বেশি নয়, তবে ছেলে-ছোকরাও নয়।
তারক তার মনিবকে দেখে চক্ষু চড়কগাছ করে বলল, “এ কী স্যার?”
গোবিন্দ বাথরুমের দিকে ইশারা করে বলল, “জল আছে?”
বাথরুমে ঢুকে লাইফবয় সাবান মেখে স্নান করে ফেলল গোবিন্দ। চেম্বারে তোয়ালে থাকে। একটা অ্যাপ্রনও। অপ্রনের ব্যবহার বড় একটা হয় না। আজ সেই অ্যাপ্রনই লজ্জা বাঁচাল। স্নানের পর পরনে তোয়ালে আর গায়ে অ্যাপ্রন চাপিয়ে গোবিন্দ তার ছোট চেম্বারে গিয়ে বসল। প্রথমেই ফোন করল বাড়িতে—“তুরন্ত জামা-প্যান্ট পাঠাও।”
মা বললেন, “তারক খবর দিয়েছে। কী হয়েছে তোর?”
গোবিন্দ বলল, “বাড়ি গিয়ে বলব।”
গোবিন্দ ফাঁকিবাজ ডাক্তার নয়। সকাল আটটা থেকে যারা এসে হাঁ করে বসে আছে ডিসপেনসারিতে তাদের তাড়িয়ে দিতে পারে না। তার এখন পায়ের তলায় জমি শক্ত করার লড়াই। মাত্র এক বছরের প্র্যাকটিস। বাজার জমাতে হবে। নিম্নাঙ্গে তোয়ালে আর উধ্বাঙ্গে অ্যাপ্রন চাপিয়ে সে রোগী দেখল। তবে চেয়ার ছেড়ে উঠল না ; পাছে তোয়ালে খসে যায়।
রোগীরা জিজ্ঞেস করল, “কি হয়েছে, ডাক্তারবাবু?”
“কিছু না। সাইকেল থেকে পড়ে গিয়েছিলাম …কালকে রাত্তিরে জ্বর কত ছিল? কাশি-টাশি হয়েছিল? সিরাপটা খেয়েছিলেন?”
রোগীদের চটপট হটিয়ে দিয়ে গোবিন্দ সবে পিঠ হেলিয়ে বসেছে এমন সময় তার মাসতুতো ভাই সুজন এসে হাজির। বাড়ি থেকে আসছে, হাতে কাগজে মোড়া প্যান্ট শার্ট। এসে বলল, “কিরে, কী হয়েছে তোর?”
গোবিন্দ হঠাৎ ফেটে পড়ে বলল, “আই উইল টিচ দেম এ লেসন।”
“কিন্তু ব্যাপারটা কী?”
“দে, আগে লজ্জা বাঁচাই।”
প্যান্ট জামা পরা হয়ে যাবার পর তারককে ডাকল গোবিন্দ। চা আর সিগারেট চাই। সুজনের কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে ধরাল। বলল, “তুই এখানকার কিছু চিনিস না। বুঝতে পারবি না। তবে কথাটা হল, পুরনো বাজারের ঠিক পরেই তেঁতুলতলার মোড়ে একটা শার্প টার্ন আছে। একপাশে এঁদো পুকুর আর খাটাল। উল্টো দিকে কোন বেটার এক মোকাম তৈরি হচ্ছে। রাস্তাটা ভাঙা-চোরা, সরু। ওই জায়গায় আর একটু হলেই গাড়ি চাপা পড়তাম মাইরি।”
“গাড়ি চাপা? বলিস কি! এই শহরে গাড়ি চাপা?”
“কেন, এ শহরটা কি ফেলনা! তোদের রানিগঞ্জের চেয়ে টেন টাইমস বেটার।”
“তা হল কী?”
“হল এই যে, একটা মেয়ে ভাই গাড়ি চালিয়ে এসে প্রায় মেরে দিয়েছিল। কোনো গতিকে প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে প্রথমে খাটাল, তারপর সুরকির গাদায়।”
“দু’দিকেই পড়লি কি করে?”
“পেছন থেকে তাড়া করল যে, আমি খাটালে—আর আমার সাইকেল সুরকির গাদায়।”
“কিছু বললি না?”
“বলবার অবস্থা রেখেছিল! সামলে উঠতে উঠতে পালাল। যাবার সময় হাসতে হাসতে বলল, সরি।”
সুজন জোরে সিগারেট টানল, “তোদের এই শহরে মেয়েরা গাড়ি চালায়?”
“না। আমি লাইফে দেখিনি। এটা হালে আমদানি, কোন রেল অফিসারের মেয়ে। দাসসাহেব।”
“গাড়ির লাইসেন্স আছে?”
“আই ডোন্ট থিংক।”
“তা হলে থানায় খবর দে, সুজন বলল।
“থানা?”
“লাইসেন্স নেই গাড়ি চালাচ্ছে। মানুষ চাপা দিচ্ছে. …এ তো অফেন্স। “
গোবিন্দ কি যেন ভাবল, তারপর বলল, “থানায়-ফানায় যাওয়া ঠিক নয়। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা, থানা মাড়ালে আঠাশ ঝামেলা। তা ছাড়া একটা মেয়ের নামে থানায় লাগানো বিচ্ছিরি ব্যাপার।”
সুজন ভাইয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারা সমবয়স্ক এবং বন্ধু। সুজন ঠাট্টা করে বলল, “তা হলে আর কী করবি, গাড়ি চাপা পড়।”
গোবিন্দ অপ্রস্তুত হয়ে বলল, “না না, এটা অন্যায়। আমার বলে কথা নয়, যে কোনো লোককেই চাপা দিতে পারে, শি ইজ ডেনজারাস। “
তারক চা সিগারেট আনিয়ে দিল।
গোবিন্দ বলল, “ভাল করে ভেবে দেখতে হবে কী করা যায়—”
সন্ধের পর, রাত্রের দিকে গোবিন্দর রোগীপত্র বড় থাকে না। সে নতুন ডাক্তার। এই শহরের ছেলে বলে একেবারে মাছি তাড়াবার অবস্থা হয়নি, নয়ত পুরনো চার পাঁচজন ডাক্তারের খপ্পর থেকে রোগী ছিনিয়ে নেওয়া সহজ ছিল না। অবশ্য গোবিন্দর বন্ধুরা তাকে সাহায্য করেছিল খুব। এখনও করে যাচ্ছে। গোবিন্দর ঢাক পিটিয়ে বেড়ানোই তাদের কাজ।
রাত্রের দিকে এই বন্ধুরা গোবিন্দের ডিসপেনসারিতে আড্ডা মারতে আসে। চা, মুড়ি, তেলেভাজা, সিগারেট, তাস খোশগল্প চলে প্রায় দশটা পর্যন্ত। তারপর যে যার বাড়ি ফিরে যায়।
সেদিন মানিক, শাঁটুল আর কল্যাণ এসেছিল। সুজন তো ছিলই।
বন্ধুদের কাছে সকালের ঘটনাটা নিবেদন করল গোবিন্দ। বলল, “খুব ন্যারোলি এস্কেপ করে গিয়েছি। লাগলে কোমর থেঁতলে যেত।”
শাঁটুল লাফ মেরে বলল, “আরে ওই তো দাসসাহেবের মেয়ে, বিউটি দাস।”
“বিউটি?”
“হ্যাঁ রে শালা, বিউটি। বাড়িতে সবাই বিউটি বলে। ভাল নাম জানি না। শুনেছি আর্কিটেক্ট। পাস করা।”
“যা যা—!”
“যা যা নয় ; একটা কিছু পাস করেছে ঠিকই।”
“মেয়েরা আর্কিটেক্ট হয় না”, গোবিন্দ মাথা নেড়ে বলল।
“হু নোজ…! আজকাল মেয়েরা কি না হয়। পাইলট পর্যন্ত হয় প্লেনের। সেদিন আর নেই জিজি যে মেয়েরা বাড়িতে বসে কাঁথা সেলাই করবে।” শাঁটুল বলল। সে মাঝে মাঝে গোবিন্দকে জিজি বলে, কেননা গোবিন্দর পুরো নাম গোবিন্দ গোপাল।
মানিক বলল, “বিউটি না বিচুটি রে?”
সুজন বেজায় জোরে হেসে উঠল।
“কিন্তু সকালের ঘটনার কী করা হবে?”
মানিক বলল, “দাসসাহেবের বাংলোয় ফোন কর।”
“ফোন করে—?”
“বিচুটিকে বল, বেশি পিঁয়াজি করলে ট্রাবলে পড়তে হবে। এটা আমাদের শহর। বেলাইন হলেই কুরুকুল চেপে পড়ব।”
গোবিন্দ বলল, “না, না, ফোন-টোন আবার কেন!”
“তা হলে?”
“ভেবে দেখ।”
বন্ধুরা ভাবতে লাগল।
দুই
গোবিন্দ শান্তশিষ্ট ধরনের ছেলে। সেদিনের ঘটনাটা সে অনায়াসেই ভুলে যেত। ফোস্কার মতন রাগও বেশিদিন গায়ে থাকে না। কিন্তু তার কপাল মন্দ। যদিও গোবিন্দ আর গাড়ি চাপা পড়ল না, কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যে সে আরও বার দুই বিউটির মুখোমুখি হল। একবার, একেবারে বাজারের মধ্যেই ; আর-একবার রেল বাংলোর দিকে। বাজারে গোবিন্দ সাইকেল চড়ে যাচ্ছে, হঠাৎ পিছনে টি টি হর্ন। রাস্তা ছেড়ে দিয়েও বাঁচল না। পিছনের গাড়ি তাকে প্রায় সবজিওয়ালাদের গায়ে ফেলে চলে গেল। যাবার সময় বিউটি জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলল, “কালা নাকি?”
আর রেল বাংলোর রাস্তায় পাশ কাটিয়ে যাবার সময় বিউটি শুধু হাসল। তার হাসিটাই এত খারাপ যে গোবিন্দর মতন শান্ত ধাতের ছেলের পিত্তি জ্বলে গেল। মেয়েটার স্পর্ধা তো কম নয়, গোবিন্দকে নিয়ে তামাশা করছে! এই শহর গোবিন্দর। তুমি কোথেকে উড়ে এসে এখানে ডাঁট মেরে যাবে।
রাত্রে বন্ধুদের কাছে গোবিন্দ জেহাদ ঘোষণা করে বলল, “আমায় গাড়ি দেখাচ্ছে! রেলের পেটি অফিসারের মেয়ের এত গরম! আমার বাপ ওরকম দশটা ফচকে গাড়ি কেনার টাকা রেখে গেছে। গাড়ি আমিও চড়েছি। দেখে নেব তোমায়।”
শাঁটুল বলল, “কী করবি?”
গোবিন্দ বলল, “গাড়ি কিনব।”
টেবিলের ওপর ঘুষি মেরে শাঁটুল বলল, “সাবাস শালা। জবাব নেই। একেই বলে মরদ। জিজি তোর মাথায় সাঙ্ঘাতিক বুদ্ধি খেলে। কেন, একটা বিশাল গাড়ি কেন। গাড়িতে গাড়িতে লাগিয়ে দে। হয় শালা আমরা মরি, না হয় বিউটিকে মারি।”
মানিক বলল, “না ভাই মারতে রাজি নই ; পুলিশ ধরবে। মরতেও পারব না—বউ কেঁদে কেঁদে মরবে।”
শাঁটুল ঝপ করে বলল, “তোর বউকে কাঁদতে দেব না মানকে। ভাবিস না।”
আড়চোখে চেয়ে শাঁটুলকে দেখল মানিক ; বলল, “আমার বউটাকে তুই টারগেট করেই থাক শালা ; কোননা লাভ হবে না।”
হাসাহাসির মধ্যে সুজন বলল, “গাড়ির আইডিয়াটা ভাল। নতুন।”
শাঁটুল বলল, “একেই সামনে সামনে লড়াই বলে। আগের দিনে এই রকম যুদ্ধ হত। তরোয়াল তো তরোয়াল। গদা তো গদা।”
গোবিন্দ বলল, “তা বলে তুমি ভেবো না—আমি একটা বিস্কুটের টিন কিনব। বড় গাড়ি কিনব, বড়। হেভি।”
ট্রাক?”
“না। বড় গাড়ি। এমনি গাড়ি। গদিঅলা গাড়ি। বসার গাড়ি। ”
মানিক তুড়ি বাজিয়ে বলল, “টেরিফিক হবে। সত্যি গোবিন্দ, তুই একটা গাড়ি কেন। আমরা চাপি। দিন কতক হইহই করি। একদিন শালা পিকনিক করে আসব তোর গাড়িতে চেপে।”
“মাল খাব,” শাঁটুল বলল।
গোবিন্দ বলল, “গাড়ি কিনব, তারপর দেখব—বিচুটি বিবির কত তেল!”
গাড়ি কেনাই সাব্যস্ত করে ফেলল গোবিন্দ।
সুজন আর গোবিন্দ দিন দুই পরামর্শ করল। নতুন গাড়ি কেনার অর্থ হয় না। তা ছাড়া শখ করার জন্যে নয়, শৌখিনতা করার জন্যেও নয়—নিতান্ত একটা মেয়ের শয়তানি ভাঙার জন্যে গাড়ি। কাজেই খরচাটা দেখতে হবে।
সুজন বলল, “তেলের দাম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরনো গাড়িগুলো লোহার দরে বিক্রি হয়ে গেছে। রানিগঞ্জের আশেপাশে কোলিয়ারিতে খুঁজলে এখনো দু’ একটা ফোর্ড, ক্যাডিলাক পাওয়া যেতে পারে। দামে ভেরি চিপ। একটু ঠকে ঠাকে নিলে জব্বর হবে।”
গোবিন্দ রাজি হয়ে গেল। তাদের এখানে মাখনের গ্যারাজ আছে। মিস্ত্রি ভাল, সব যন্ত্রই সারাতে পারে—মায় হারমোনিয়াম পর্যন্ত। লোক বলে বিশ্বকর্মার বাচ্চা।
কিন্তু ড্রাইভার? সেটার তেমন সমস্যা নয়, শাঁটুলের চেনা-জানা ড্রাইভার আছে—ধরে আনবে।
গোবিন্দর মা বললেন, “ভাঙাচোরা গাড়ি কিনবি কেন? কিনলে ভাল দেখে কেন। ডাক্তার মানুষ একটা গাড়ি থাকলে দূরেও রোগী দেখতে যেতে পারবি।”
সুজন ফক্কুড়ি করে বলল, “ভাল গাড়ি শ্বশুর দেবে, গোবিন্দর বয়ে গেছে কিনতে।”
তিন
দিন পনেরো বিশ পরে এক ট্রাকের পিছনে দড়ি বেঁধে একটা গাড়ি এনে হাজির করল সুজন। যেন মালগাড়ি একটা। ডজ গাড়ি। বেশ পুরনো। চাকা চারটে ঠিকই আছে। একবার গ্যারাজে দিলেই গাড়ি গর্জন করে উঠবে।
গোবিন্দ গাড়ির বহর দেখে খুশি হলেও চেহারা দেখে সন্তুষ্ট হল না। বলল, “সুজন, সামনে দুটো মোষ জুততে হবে নাকি রে? এ গাড়ি চলবে?”
“ওর বাপ চলবে। তবে এ সব গাড়ির নিয়ম হল মাঝে মাঝে চলা, চলতে চলতে থামা। একনাগাড়ে চলতে পারবে না। বুড়ো হাড়। ম্যানেজ করে নেবে।”
শাঁটুল আর মানিক গাড়ি দেখে বলল, “ও শালা, একেবারে সার্কাসের হাতি। খাসা হয়েছে। খুঁটিতে বেঁধে রাখলেও আনন্দ। নে গোবিন্দ, মাখনকে ডাক। জলদি ঠিক করে ফেলুক।”
ডাক পড়ল মাখনের। ঝানু মিস্ত্রি। দেখে-টেখে বলল, “এ হল বনেদি গাড়ি। কলকবজা মেরামত করে নিলে চলবে। তবে খাবে বেশি। দিন, ঠিক করে দি। তবে বাবু, গদি আর রং পালটে নিতে হবে। নষ্ট হয়ে গেছে।”
গোবিন্দ সেদিন সকালেই আবার বিউটির হাসি শুনেছে রাস্তায় ; মেজাজ গরম ছিল। বলল, “কুছ পরোয়া নেই। এ গাড়ি রাস্তায় চালাতেই হবে মাখনদা, তোমার হাতে কোন গাড়ি না চলেছে।”
বাজার থেকে কুলিকাবারি ডেকে এনে মাখন মিস্ত্রি গাড়ি নিয়ে চলে গেল। বলল, মাসখানেক সময় লাগবে। মানে, পুজোর আগে দিয়ে দেবে গাড়ি।
ইতিমধ্যে কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে। বিউটি দাসের সঙ্গে গোবিন্দর দেখা হয়েছে দু বার। একবার গোবিন্দর বাড়ির সামনেই, কোথাও গিয়েছিল বিউটি। একলা। ফেরার পথে তার গাড়ির চাকা পাংচার হয়ে রাস্তায় পড়ে আছে। বিউটি রাস্তায় দাঁড়িয়ে। পরনে মেয়ে প্যান্ট আর শার্ট। মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত। পায়ে চটি। চোখে সানগ্লাস। রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিউটি লোক খুঁজছিল। চাকা পালটাতে হবে। গোবিন্দ সবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সাইকেলে উঠবে, বিশ পঁচিশ গজ দূরে বিউটিকে দেখে থ। বিউটির এমন বেশও আগে দেখেনি। ব্যাপারটা বুঝে গোবিন্দর বগল বাজিয়ে নাচতে ইচ্ছে হল। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। কাজেই সে সটান চলে যাচ্ছিল। বিউটি রাস্তায় লোক খুঁজছে। গোবিন্দকে হাতে তালি বাজিয়ে ডাকল। গোবিন্দ শুনল না। সাইকেলের ঘন্টি বাজাতে বাজাতে চলে গেল।
আর একবার দেখা হয়েছিল গোবিন্দর ডিসপেনসারির কাছে। বিউটির গাড়ির হর্ন আটকে গেছে। থামছে না! বেজেই চলেছে তারস্বরে। গাড়ির বনেট খুলে বিউটি নিজেই কি যেন করছে। লোক জমে গেছে আশেপাশে। গোবিন্দকে দেখে বিউটি কড়া চোখে তাকাল।
এই দুটো ঘটনাই গোবিন্দকে যৎপরোনাস্তি খুশি করেছিল। বন্ধুদের কাছে বলেছিল—জোর জব্দ হয়েছে বিউটি।
শাঁটুল করিতকর্মা ছেলে। সে এর মধ্যে বিউটি দাসের ঠিকুজি কোষ্ঠী জেনে ফেলেছে। দাসসাহেবের দুই মেয়ে বিউটি আর আংটি। একটি ছেলে। বিউটি সবার বড়। সত্যি সত্যি মেয়েটা আর্কিটেক্ট, কোথা থেকে যেন পাসও করেছে। বিয়ে হয়নি, হব হব করছে। দাসসাহেব আর দাসগিন্নি দুজনেই, মানুষ ভাল। তবে মেয়ে অন্ত প্রাণ। মেয়ে যা চায় তাই পায়। দাসগিন্নি মোটেই পছন্দ করেন না মেয়ে গাড়ি চালিয়ে ঘুরে বেড়াক, কোথায় কি অঘটন ঘটবে—তখন বিয়ে দিতে পারবেন না মেয়ের। তার চেয়ে ভোঁদা ড্রাইভারকে নিয়ে ও ঘুরুক না কেন। মেয়ে সে-কথা শোনে না। গাড়ি সে নিজেই চালাবে। তিন বছর ধরে চালাচ্ছে। লাইসেন্স পেয়েছে একবারে।
সব শুনে-টুনে মানিক বলল, “শাঁটুল, তুই কোনো রকমে একটা এনট্রি নিয়ে ফেল দাস ফ্যামিলিতে। তারপর জাল ছিঁড়ে বের হয়ে আসবি।”
শাঁটুল বলল, “খুব চেষ্টা করছি। আমার মার মাসির মামাতো বোনের ভাশুর-ঝি গোছের একটা সম্পর্ক পাচ্ছি দাসগিন্নির। কিছু একটা পাতাতে না পারলে ঢুকি কি করে?”
চার
মাখন মিস্ত্রির গ্যারেজে গোবিন্দর ডজ তৈরি হচ্ছিল। গোবিন্দ বন্ধুবান্ধব নিয়ে প্রায়ই দেখতে যেত। ছেলেবেলায় দুর্গাপুজোর আগে প্রতিমার খড় বাঁধা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন গোবিন্দরা রোজ ছুটে ছুটে ঠাকুর তৈরি দেখতে যেত, একেবারে সেই ভাবে গোবিন্দ আর শাঁটুলরা আসা যাওয়া শুরু করল গ্যারাজে।
মাখন মিস্ত্রি মিথ্যে বলেনি ; খুঁজে খুঁজে, জোড়াতালি মেরে মালপত্র জুটিয়ে গাড়িটাকে চালু করে দিল। মানে রীতিমত আওয়াজ করে গাড়ির ইঞ্জিন চলল। ইঞ্জিন আওয়াজ মারতেই শাঁটুল মাথার ওপর হাত তুলে নাচতে লাগল। গোবিন্দ বেজায় খুশি। মানিক বলল, “ফেরার সময় বাজারে কালীতলায় পুজো দিয়ে যাব।”
এখনও কিছু কাজ বাকি যন্ত্রপাতির। রং বাকি, গদি বাকি। এদিকে মহালয়া এসে পড়েছে। গোবিন্দ বলল, “মাখনদা, কুছ পরোয়া নেই ; যা চাও পাবে, ফিনিশ করে দাও। ষষ্ঠীপুজোর আগের দিন গাড়ি চাই।”
মাখন বলল, “রং কি হবে বাবু?”
মানিক বলল, “ব্রাইট রং। লাল, নীল।”
শাঁটুল বলল, “না না, লাল-ফাল নয়। কেলো ষাঁড় লাল দেখলে ভাববে তার . কমপিটিটার এসেছে। হলুদ হোক।”
গোবিন্দ বলল, “হলুদ আবার রং নাকি?”
শাঁটুল বলল, “গাত্রহরিদ্রা বলে একটা কথা আছে না—তাই বলছিলাম।”
মানিক ধমক দিয়ে বলল, “শালা, এটা কি গোবিন্দর গায়ে হলুদের তত্ত্ব। যত সব মাথামোটা ব্যাপার।”
শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, মালটিকালার রং হবে। মানে লাল, হলুদ, কালো, নীল—সব মিলিয়ে। এমন রং হবে—যাতে এক মাইল দূর থেকেও মনে হবে—একটা গাড়ি আসছে। আজকাল আমেরিকায় এ রকম বেখাপ্পা রং করে ডিজাইনের পুরনো ধারণা ভেঙে ফেলা হচ্ছে।
গোবিন্দ বলল, “ঠিক আছে, লাগাও। তবে একটু দেখেশুনে।”
শাঁটুল বলল, “তুই ভাবিস না ; আমি রং দেখব। জেব্রা ডিজাইনের মতন রং লাগাব।”
ষষ্ঠীপুজোর দিন গাড়ির ট্রায়াল হল ফাঁকায় গিয়ে। একেবারে জাত গাড়ি। আওয়াজে সেটা মালুম দিল। লম্ফ-ঝম্ফও করল মন্দ নয়। রাস্তার কিছু কুকুর অবশ্য বহু রঙের সংমিশ্রণে তৈরি গাড়ির ডিজাইনটা বোঝেনি। তারা দলে দলে ভিড় করেছিল, চেঁচামেচি করেছিল। কিন্তু কুকুরদেরও বোধবুদ্ধি আছে। যে মুহূর্তে বুঝল, ওটা গাড়ি, আকাশের দিকে মুখ করে সমস্বরে ডাক দিল, যেন অভ্যর্থনা জানাল গাড়িটাকে। তারপর লেজ গুটিয়ে পালাল। একটা অসুবিধে অবশ্য থেকে গেল। হর্ন পাওয়া গেল না। একটা প্যাক প্যাক হর্ন লাগাতে হল। তাতেই সুবিধে।
বাড়িতে গাড়ি আসতেই গোবিন্দর মা বললেন, “ছি ছি, টাকাগুলো নষ্ট করলি।”
গোবিন্দ বলল, “দেখো না কেমন চলে। এ শহরে এত বড় গাড়ি কারুর নেই। যাও তুমি পুজো দিয়ে এসো গাড়ি চেপে। …সুজন এসেছে?”
“না।”
“ইডিয়েট, আজ তার আসার কথা। এখানে থাকবে দেওয়ালি পর্যন্ত।”
“আসবে হয়তো বিকেলে। “
গাড়ির কিছু ধোওয়া-ধুয়ি বাকি ছিল। চাকরবাকর দিয়ে গাড়ি ধোওয়াল মিশির। শাঁটুল ড্রাইভার হিসেবে মিশিরকে জুটিয়ে দিয়েছে। মিশির মস্ত ড্রাইভার, ভাড়া লরি চালাত ; এখন বয়স হয়ে গিয়েছে, আর তেমন খাটতে পারে না। মিশিরের সঙ্গে শর্ত, এক মাসের মধ্যে গোবিন্দকে গাড়ি চালানো শিখিয়ে দেবে।
গোবিন্দর মা গাড়ি চেপে পুজো দিয়ে এসে বললেন, “তোর গাড়ি দেখতে মেলা বসে গেল রে গোবিন্দ।”
গোবিন্দ বলল, “কেমন চলল?”
“চলতে চলতে বন্ধ হয়ে যায়।”
“নতুন নতুন হবে।”
মা আর কিছু বললেন না।
সুজন বিকেলের দিকে এসে পৌঁছল। গাড়ি দেখে বলল, “ফেরোসাস। বন থেকে বাঘের মতন বেরিয়ে এসেছে। কী শো?..সেই বিচুটি দেখেছে?”
“না ; এইবার দেখাব। ..আয় তোর গাড়ি নিয়ে, মারব ধাক্কা ছিটকে পড়বি।”
“একেবারে মেরে ফেলিস না, পুলিশ কেস হয়ে যাবে।”
গোবিন্দ বলল, “দেখ না, বিচুটির কী হাল করি।”
রাত্রে রোগী দেখার পাট চুকিয়ে চা খেতে খেতে বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ হল, বিউটিকে কোথায় কোথায় কখন ধরা যায়। শাঁটুল কাগজ কলম নিয়ে একটা চার্ট এঁকে ফেলল রাস্তাঘাটের। কোন কোন রাস্তায় বিউটি গাড়ি ছুটিয়ে ঘুরে বেড়ায়, কোথায় কখন তাকে দেখা যায়। পুজোর সময় কোথায় কোথায় পাওয়া যেতে পারে।
শাঁটুলের প্ল্যানই শুধরে সাব্যস্ত হল, কাল থেকেই গোবিন্দ তার গাড়ি নিয়ে বিউটিকে গুঁতোতে বেরুবে। অবশ্য কখনও গুঁতোবে, কখনও রাস্তা আটকে দেবে, কখনও মুখোমুখি তেড়ে যাবে।
শাটুল বলল, “জিজি, এবার তোর কেরামতি দেখব।”
গোবিন্দ গোপাল বলল, “দেখে নিবি।”
পাঁচ
সপ্তমী পুজোর দিন সকালেই প্রথম সংঘর্ষ। বাজারের বাইরে। বিউটির ছোট গাড়ির মুখোমুখি তেড়ে গিয়ে গোবিন্দর সেই বিচিত্র গাড়ি থেমে গেল। শুধু থেমে গেল নয়, বার কয়েক এমনভাবে দুলল যে মনে হল বলছে, আয় ছুঁড়ি তোর রং দেখি।
বিউটি গাড়িতে বসেই বিরক্তভাবে হর্ন দিল। গাড়ি সরাও।
গাড়ি সরল না। নড়ল না। ড্রাইভারের পাশে বসে গোবিন্দ দেখতে লাগল বিউটি কী করে।
মিশির বার কয়েক চেষ্টা করল গাড়ি নড়াবার। গাড়ি নড়ল না।
দরজা খুলে বেরিয়ে এল বিউটি। পরনে আজ শাড়ি ব্লাউজ। ফাঁপানো বব চুল। সটান গোবিন্দর গাড়ির কাছে এসে বলল, “গাড়ি না গন্ধমাদন?”
গোবিন্দ বলল, “ডজ!”
“ডজ না গজ! গাড়ি সরান।”
“আপনি আপনারটা সরিয়ে নিয়ে যান না।”
“কোথায় সরাব! একটা আদ্যিকালের লজঝড় গাড়ি এনে রাস্তা বন্ধ করে রেখেছেন দেখতে পাচ্ছেন না! যেমন মালিক তার তেমনি গাড়ি।”
গোবিন্দ স্মার্টভাবে বলল, “ওটা দু’ পক্ষই সমান।”
“মানে?”
“বুঝে নিন।”
“হ্যাং ইওর বুঝে নিন। ননসেন্স।”
“ইডিয়েট।”
“শাট আপ।”
“ইউ শাট আপ।”
লোক জমে যাচ্ছিল রাস্তায়। হঠাৎ মিশির আবার স্টার্ট দিতেই গাড়ি যাব যাব ভাব করল। গাড়ি সরিয়ে নিল মিশির।
বিউটি চড় দেখিয়ে চলে গেল। বলল, “দেখে নেব আপনাকে। অসভ্য ব্রুট!”
গোবিন্দ বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, “যাও যাও আমার কাঁচকলা করবে। আমার দু’ পুরুষের বাস এই শহরে। ”
ডিসপেনসারিতে এসেই গোবিন্দ শাঁটুলদের খবর দিতে লোক পাঠাল। সুজনকে ডাকল ফোনে।
রোগীদের চটপট ছেড়ে দিল গোবিন্দ। মিক্সচারগুলো রিপিট করে দিল। কারও কাছ থেকে একটা পয়সা নিল না। পুজোর ক’দিন সে ফ্রি দেখে।
সামান্য বেলায় শাঁটুল সুজন মানিক চলে এল।
গোবিন্দ সকালের ঘটনা বলল।
শাঁটুল নাচতে লাগল। জয় মা জগদম্বা। দুর্গা মাই ফেভার করেছে রে জিজি। লেগে যা শালা। পেছনে লেগে থাক।
মানিক বলল, “না, কোনো মেয়ের পেছনে লাগার জন্যে আমরা নয়। আমি বলি কি গোবিন্দ, এবার তুই পাশ থেকে লাগ।”
“মানে?”
“পাশে গিয়ে পুশ করবি।”
“ওর গাড়ি তুবড়ে যাবে।”
“দে না, তুবড়ে দে।”
সুজন বলল, “না না, এখনই তোবড়া-তুবড়ি কেন? এখন কিছুদিন ব্লকেড চলুক। তারপর সময় বুঝে পুশ।”
অষ্টমী পুজোর দিন শাঁটুলের প্ল্যান মতন গোবিন্দ বিশেষ জায়গায় বিউটিকে পাকড়াবার চেষ্টা করল। পারল না। পাত্তা পেল না বিউটির। রাত্রে শাঁটুল বলল, “ভড়কে গিয়েছে রে। রিট্রিট। এক দিনেই।”
নবমী পুজোর দিন সকালে গোবিন্দ ডাক্তারখানায় আসার পথে দূরে বিউটির গাড়ি দেখতে পেল। মিশিরকে বলল, তাড়া করতে। কাছে গিয়ে গোবিন্দ দেখল, গাড়ির মধ্যে প্রবীণা মহিলা, গরদের শাড়ি পরনে, পুজোর জিনিসপত্র রয়েছে পাশে। সামনে বিউটি, স্নান করে সাদা সিল্কের শাড়ি পরেছে, লাল ব্লাউজ। সঙ্গে তার ছোট ভাই। গোবিন্দ বুঝতে পারল, দাসগিন্নি বাজার ঘুরে পুজোমণ্ডপে যাচ্ছেন পুজো দিতে। গোবিন্দ সংকোচ বোধ করল। এখানে কিছু করা যায় না। মিশিরকে বলল, গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে। অবশ্য ওরই মধ্যে বিউটির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেছে গোবিন্দর। বিউটি কড়া চোখে তাকিয়েছে, নাক সিঁটকেছে, তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে।
রাত্রে পুজোমণ্ডপে দলবল নিয়ে গিয়েছিল গোবিন্দ। দাস-পরিবারকেও দেখল তারা ; কর্তাগিন্নি ছেলেমেয়ে সবাই এসেছে। দাসসাহেবের চারপাশে জোঁকের মতন লেগে আছে পুজো কমিটির মাতব্বররা। বিউটি মেয়েদের স্টলে হাসাহাসি করছে। বেলুন ফাটাচ্ছে।
শাঁটুল বড় শয়তান। কোথা থেকে দু’ পাতা কালী পটকা এনে একসঙ্গে ফাটিয়ে দিল। বিউটি স্টলের মধ্যে ঢুকে পড়ল লাফ মেরে।
তারপর আচমকা মুখোমুখি। গোবিন্দকে দেখেই বিউটি দাঁতে দাঁত চেপে বলল, “স্কাউড্রেল। ”
গোবিন্দ বলল, “লবেজান বিবি।”
বিউটি লাল হয়ে বলল, “বিস্ট। বিস্ট।”
পুজোটা এইভাবে কাটল। গোবিন্দ তার নোট বুকে একটা চার্ট তৈরি করেছিল। ফুটবলের লিগ টেবিলের মতন। তাতে লেখা ছিল, ক’বার এনকাউন্টার হয়েছে বিউটির সঙ্গে, কে জিতেছে, কে হেরেছে, ক’বার দুপক্ষই সমান গিয়েছে। বন্ধুদের চার্টটা দেখাত গোবিন্দ। তাতে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, চব্বিশবার মুখোমুখি হয়েছে গোবিন্দ আর বিউটি ; ওপক্ষ জিতেছে দশবার, গোবিন্দ আটবার। ছ বার ড্র।
শাঁটুল বলল, “তুই বেটা পিছিয়ে আছিস। শেম। মেক ইট ইক্যুয়াল। ”
এই সব করতে করতে পুজো পেরিয়ে দেওয়ালি এসে গেল। এর মধ্যে গোবিন্দর গাড়ি শহরের মানুষের কাছে বিখ্যাত হয়ে গেছে। নানা রকম নাম দিয়েছে লোকে গাড়িটার। কেউ বলে, গোবিন্দর রথ, কেউ বলে ঠেলাগাড়ি, কেউ বলে শালা ট্যাংক যেন। গাড়িটা চলছে বটে, তবে তার নানা ব্যাধি। যখন তখন বন্ধ হয়। যেতে যেতে ঝাঁকি মারে, যেন পেছনের পা তুলে ঘোড়া নাচছে। বিস্তর ধোঁয়া ছাড়ে। গর্জনও বিরাট। মাখন মিস্ত্রি ঠকঠাক করেই যাচ্ছে অনবরত। মিশির বলেছিল, ডাক্তারবাবুকে গাড়ি চালানো শিখিয়ে দেবে। সেই শিক্ষাপর্ব চলছিল।
একদিন সকালের দিকে ফুটবল মাঠে নিয়ে গিয়ে মিশির গোবিন্দকে গাড়ি চালানো শেখাচ্ছে, হঠাৎ ধূমকেতুর মতন বিউটির আবিভাব। রাস্তা থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখল। হর্ন মারল তারপর পালাল।
গোবিন্দ বড়ই মর্মাহত হল। আবার দু’ পয়েন্ট নষ্ট হল।
রাত্রে বন্ধুরা এলে গোবিন্দ বিমর্ষ হয়ে বলল, “শাঁটুল, আমার দ্বারা হবে না।”
শাঁটুল বলল, “বলিস কি! উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ?”
“বাট আই অ্যাম লুজিং দি গেম।”
“নেভার। আমরা রয়েছি কেন!…শোন জিজি, দাসগিন্নির সঙ্গে আমরা ভাব হয়ে গেছে। বাতের রুগি। হাঁটুতে বাত। আমি বলেছি, আমার বন্ধু জিজিকে দেখান মাসিমা। ও হল আর এস।”
“আর এস?”
“রিউম্যাটিজম স্পেশ্যালিস্ট।”
“শালা!”
“না রে, শালা নয়। গিন্নি ইজ ভেরি গুড। কর্তাও লোক ভাল। কর্তার একটু অর্শের ব্যামো আছে। তোকে দু’ দিক দিয়ে অ্যাটাক করতে হবে।”
মানিক বলল, “যাকে মিলিটারির ভাষায় বলে সাঁড়াশি আক্রমণ।”
গোবিন্দ মাথা নাড়ল। “না ভাই, আমি বাত কিংবা অর্শ স্পেশ্যালিস্ট নই। আমি উইথড্র করব। লেট হার উইন।”
সুজন বলল, “বংশের নাম ডোবাবি তা হলে!”
ছয়
দেওয়ালির পর সন্ধেবেলায় একদিন ডাক্তারখানায় ফোন পেল গোবিন্দ।
“জিজি, মাসিমার বাড়ি থেকে কথা বলছি।”
“মাসিমা?”
“মিসেস দাস! মাসিমার হাঁটু ফুলে গেছে। পা নাড়াতে পারছেন না। একবার দেখে যা।”
“আমি?”
“সিরিয়াস ব্যাপার। দু’ রাত্রি ঘুম হয়নি। চলে আয় ভাই, গাড়ি নিয়ে।”
গোবিন্দ কিছু বলার আগেই শাঁটুল ফোন ছেড়ে দিল।
সামান্য ভেবেচিন্তে গোবিন্দ বেরোব বেরোব করছে ; আবার ফোন।
“হ্যালো, এইচ ডি?”
“এইচ. ডি?”
“হর্সেস ডক্টর। প্লিজ ডোন্ট কাম।” বিউটির গলা।
গোবিন্দর কান মুখ গরম হয়ে উঠল। “হু আর ইউ প্লিজ?”
“দিস ইজ বিউটি স্পিকিং।”
“অ্যান্ড দিস ইজ বিস্ট অ্যানসারিং, আই অ্যাম কামিং।”
“ডোন্ট কাম।”
“আই মাস্ট।” গোবিন্দ ফোন ছেড়ে দিয়ে গলগল করে ঘামতে লাগল।
নিতান্ত কপালই বলতে হবে, গোবিন্দ দাসগিন্নির হাঁটু ফোলা এবং ব্যথা কমিয়ে ফেলতে পারল। দাসগিন্নি বললেন, “কী লক্ষ্মী ডাক্তার তুমি। ওগো শুনছ—তুমিও গোবিন্দকে দেখাও।”
দাসসাহেব বললেন, “তাই ভাবছি।”
চেম্বারে বসে আড্ডার সময় মানিক বলল, “গোবিন্দ, তুই হবু শাশুড়ির বাত আর শ্বশুরের অর্শ নিয়ে পড়লি?”
গোবিন্দ বলল, “মানে? ওরা আমার শ্বশুর শাশুড়ি হবে কেন?”
মানিক রহস্যময় হাসি হেসে বলল, “হবে হবে।”
সাত
শীত নয়, তবে শীত শীত ভাব এসে গিয়েছে তখন। হেমন্তের মাঝামাঝি। রাত্রের আড্ডায় মানিক আর শাঁটুল এল। সুজন নেই। সে ফিরে গেছে।
শাঁটুল এসে বলল, “জিজি, পরশু দিন একবার মহাবীর পাহাড়ে যাবি? মেলা দেখে আসব।”
“না।”
“পরশু তো রবিবার। সকাল ছাড়া তোর কাজ নেই।”
“অনেক দূর ; দশ বারো মাইল।”
“তাতে কি! গাড়ি নিয়ে যাবি তুই। এখন তো তুই নিজেই বেশ চালাস।”
“অনেক তেল পুড়বে।”
“নেভার মাইন্ড। আমি তেলের দাম দেব।”
“তোর মতলবটা কি?”
শাঁটুল প্রথমে ভাঙল না। তারপর বলল, “কলকাতা থেকে বিউটির এক ফ্রেন্ড এসেছে। শুনলাম—বিউটি ফ্রেন্ডকে নিয়ে মহাবীর পাহাড়ে যাবে।”
“কোন ফ্রেন্ড?”
“বয় ফ্রেন্ড।”
“তাতে আমার কি?”
“বাঃ, তোর কি! তোরই তো সব। আমার মনে হয় বিউটিকে এভাবে ফাঁকায় ছেড়ে দেওয়া যায় না। ”
“সে তার মা বাবা বুঝবে।”
“মা বাবা রাজি নয়। বিউটি শুনছে না।”
“তা আমি কি করব।”
“আমার মনে হয়, আমাদের থাকা উচিত। বিউটি যেভাবে গাড়ি ফাড়ি চালায়—একটা অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে। ফাঁকা রাস্তা। তুই ধরে নে না—আমরা অ্যামবুলেন্স ভ্যান হয়ে যাব।”
মানিক চোখ টিপে বলল, “আমারও তাই মনে হয়। হাজার হোক, অ্যামবুলেন্স তো হতেই হবে একদিন।”
গোবিন্দ খেপে গিয়ে বলল, “তোমাদের ভাল তোমাদের থাক। আমাকে কুকুর-বেড়ালের মতন ট্রিট করে। আই হেট হার।”
শাঁটুল বলল, “তুই এ-সব বললে বড় দুঃখ পাই। জিজি, তুই কত বড় বংশের ছেলে। তোর কত গুণ। তুই দয়ামায়া ভুলে যাবি, জিজি।”
শেষ পর্যন্ত গোবিন্দ রাজি হয়ে গেল।
রবিবার বিকেলে যথারীতি গোবিন্দ তার গাড়ি নিয়ে শাঁটুল মানিককে সঙ্গী করে মহাবীর পাহাড়ে গেল। যাবার পথে বিউটিকে দেখতে পেল না। মেলায় পৌঁছতে না পৌঁছতেই চোখে পড়ল বিউটি ফিরছে। ভাল করে দেখা গেল না। ভিড়ের আড়ালে পড়ে গিয়েছিল।
মেলায় একটু অপেক্ষা করেই শাঁটুল বলল, “জিজি, লেট আস গো।”
গোবিন্দ বলল, “এই তো এলাম।”
“আমার কিন্তু ভয় করছে। চল ফিরে যাই। বিউটি যেভাবে বেরিয়ে গেল।”
বাধ্য হয়েই গোবিন্দ বলল, “চল।”
গাড়িতে বসে গোবিন্দ কোথাও বিউটিকে দেখতে পেল না। কত দূর চলে গেছে কে জানে! গোবিন্দ গাড়িতে স্পিড় ওঠাতে ভয় পাচ্ছিল। একে কাঁচা হাত, তায় গাড়ি বিকল হয়ে যাবার ভয়।
পাঁচ সাত মাইল রাস্তায় গরুর গাড়ি, টাঙা, দেহাতি-বাস ছাড়া কিছু চোখে পড়ল না । মনে হল, বিউটি চলেই গেছে।
শহরে পৌঁছতে আর মাইল দুই। সেখানে এসে দেখা গেল, রাস্তার এক পাশে বিউটির গাড়ি পড়ে আছে। রাস্তায় বিউটি দাঁড়িয়ে।
গোবিন্দদের গাড়ি দেখতে পেয়েই হাত তুলল বিউটি।
শাঁটুল বলল, “দাঁড়া।”
গোবিন্দ খানিকটা এগিয়ে এসে দাঁড়াল। বলল, “আমি যাব না। তুই যা।”
নেমে গেল শাঁটুল।
মানিক বলল, “গোবিন্দ, দাসগিন্নিকে দেখছি যেন রে!”
গোবিন্দ বলল, “দাসগিন্নি কোথা থেকে আসবে?”
“দেখছি যে। বিউটির বোনও যেন আছে।”
“শাঁটুল যে বলল—”
“শালা বাজে কথা বলেছে।”
ততক্ষণ শাঁটুল ফিরে এসেছে। বলল, “জিজি, বিউটির গাড়ি আর চলছে না। অনেক চেষ্টা করেও কিছু হয়নি। গাড়িটাকে টেনে নিয়ে যেতে হবে। তোর গাড়িতে দড়ি আছে?”
গোবিন্দ বলল, “দড়ি নেই, বালতি আছে।”
“তা হলে?”
“পেছনটা দেখ। কিছু পেতেও পারিস।”
পিছনে কিন্তু দড়ি পাওয়া গেল। কেমন করে পাওয়া গেল গোবিন্দ বুঝল না।
সামনে গোবিন্দর গাড়ি। পেছনে বিউটির। দুটো গাড়িতে গাঁটছড়া বাঁধা। যেতে যেতে শাঁটুল বলল, “জিজি, তোর এত মুখ গোমড়া কেন?”
“বাজে বকিস না।”
“বাজে বকছি কোথায়! তুই কাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছিস, বোঝ। দাসগিন্নি, বিউটি, আর তোর শালা শালীকে।”
“শাট আপ, শালা। তুই আমায় ব্লাফ ঝাড়লি। ”
শাঁটুল হোহো করে হাসতে লাগল। বলল, “আমি ঝাড়লাম না বিউটি ঝাড়ল। তোকে যে কি লাভ করে বিউটি!”
গোবিন্দ চেঁচিয়ে বলল, “লাভের নিকুচি করেছে। ও আমায় বিস্ট বলেছে—তা জানিস।”
“সো হোয়াট। বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্ট!”
বিয়ের পর গোবিন্দ গাড়িটাকে ফেলে দিতে চেয়েছিল। বিউটি বলেছিল, পাগল। ওটা যত্ন করে সাজিয়ে গুজিয়ে রেখে দাও। ও জিনিস না দেখলে কে তোমায় বিয়ে করত!
গোবিন্দ গাড়িটাকে সযত্নে রেখে দিয়েছে।
বিচিত্র প্রেম
দিন চারেক হল অতুল বাড়ি ছাড়া। পাড়া ছেড়েই পালিয়ে এসেছে। যে-রকম কেচ্ছা হয়ে গেল বাড়িতে তারপর কোনো ভদ্রলোকই আর মুখ দেখাতে পারে না। অতুলও মুখ দেখাচ্ছে না। অবশ্য এই মুখ আর দেখার মতনও নেই, চারদিনেই চুপসে গেছে, গালে দাড়ি জমেছে বিস্তর, চোখে হলুদ হলুদ ছোপ ধরেছে, মাথার চুলে জটের গন্ধ। তবু এই মুখই একজনকে অন্তত না দেখালেই নয় বলে অতুল রেল স্টেশনের ডাউন প্ল্যাটফর্মের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে বসে আছে।
এখন এদিকে কোনো গাড়িটাড়ি নেই। কখনো সখনো দু একটা মালগাড়ি যাচ্ছে। যাক । অতুল প্ল্যাটফর্মের কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায় গোল করে বাঁধানো সিমেন্টের বেদিতে বসে। বসে বসে বিকেলের আকাশ দেখছে উদাস চোখে, মাঠঘাট নজর করছে বিষন্নভাবে, লম্বা লম্বা নিশ্বাস ফেলছে, সিগারেট টানছে ঘন ঘন। আর থেকে থেকে দূরে ওভারব্রিজের দিকটা লক্ষ করছে।
অতুলের অপেক্ষার অবসান হল আরও খানিকটা পরে, বিকেলের আলো যখন মাঠঘাট ছেড়ে শূন্যে উঠে পড়েছে এবং ক্রমশই ফিকে হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে—তখন।
প্রীতি কাছাকাছি আসতেই অতুল আবার বড় করে নিশ্বাস ফেলল। খুঁটিয়ে দেখতে লাগল প্রীতিকে। অতুলের মতন লণ্ডভণ্ড চেহারা নয়, মোটামুটি ফিটফাট। ছাপা শাড়ি, কলাপাতা রঙের ব্লাউজ, চোখমুখ পরিষ্কার। বাঃ, বেশ! তোফা আরামে আছ মাইরি! সত্যি, মেয়েরা একটা জিনিস। এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল, তারপরও যেমনকে তেমন, মুখে পাউডার মাখতেও ভোলেনি। অতুলের রীতিমতো অভিমান হল, কিংবা হয়তো ক্ষুব্ধই হল সে।
প্রীতি এসে সামনে দাঁড়াল। নজর করে দেখতে লাগল অতুলকে। তারপর একটা ‘ইস’ শব্দ করল, দুঃখে না বিরক্তিতে বোঝা মুশকিল।
অতুল বলল, “যাক, তা হলে এসেছ? আমি ভাবছিলাম, আসবে না।” ক্ষোভের গলাতেই বলল অতুল।
প্রীতি বলল, “বাঃ, কাজকর্ম সেরে আসব না। তা ছাড়া আমি খবরই পেলাম দুপুরে। যোগেন গিয়ে বলল, তুমি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দেখা করতে বলেছ! এত জায়গা থাকতে এই প্ল্যাটফর্ম তোমার মাথায় এল কেন জানি না , বাবা। বাড়ি থেকে কম দূর?”
অতুল গম্ভীর মুখে বলল, “প্ল্যাটফর্মই ভাল। অনেক মালগাড়ি যাচ্ছে। দু পা এগিয়ে গলাটা বাড়িয়ে দিলেই চলবে।”
প্রীতি টেরা চোখ করে কটাক্ষ হানল। বলল, “আহা—কী কথা রে।”
অতুল একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। প্রীতি ততক্ষণে পাশে বসেছে।
“তোমার মার খবর কী?” অতুল জিজ্ঞেস করল।
“মা ভাল হয়ে গেছে। …তবে বেশ গম্ভীর। কথাবার্তা বেশি বলে না।”
অতুল একটু চুপ করে থেকে বলল, “কেরাসিন তেলের এফেক্ট। বোধ হয় এখনও স্টমাক থেকে তেলের গন্ধ উঠছে।”
প্রীতি আড়চোখে দেখল অতুলকে। বলল, “তোমার বাবার খবর রাখ?”
“শুনেছি ভাল আছে।”
“শুধু ভাল কেন, সেই বুড়ো তো লাফ মেরে মেরে নাচছে..বগল বাজাচ্ছে।”
অতুল ঘাড় ফিরিয়ে প্রীতির দিকে তাকাল। শ্লেষের গলায় বলল, “কথাগুলো কে শিখিয়ে দিয়েছে? তোমার মা?”
প্রীতির মাথা গরম হয়ে উঠল। “আমার মা যা শিখিয়েছে তোমার বাবা তোমাকে তার চেয়েও বেশি শিখিয়েছে।”
অতুল সিগারেটের টুকরোটা রাগের মাথায় ছুড়ে ফেলে দিল। “আমার বাবা সম্পর্কে একটা রেসপেক্ট আমি তোমার কাছে আশা করি। নিজের শ্বশুর সম্পর্কে তোমার যে সব কথাবার্তা, বুড়ো লাফ মেরে মেরে নাচছে, বগল বাজাচ্ছে…ছি ছি…এসব কথা কানেও শোনা যায় না।”
প্রীতি বাঁ হাতটা মুঠো করে বুড়ো আঙুল দেখাল। “তোমার বাবা আমার শ্বশুর? বয়ে গেছে আমার। তোমার বাবা আমার ইয়ে—” বলে বুড়ো আঙুল নাড়াতে লাগল।
অতুল একেবারে থ’। কান কপাল গরম হয়ে উঠতে লাগল। সামান্য তোতলানো জিবে অতুল বলল, “আমার বাবা তোমার শ্বশুর নয়?”
‘না।’
“অফিসিয়ালি নয়, কিন্তু আন-অফিসিয়ালি তো বটে।”
“মোটেই নয়। অমন লোককে আমি শ্বশুর করব না। একটা সত্তর বছরের বুড়ো—দুটো ঘুমের বড়ি খেয়ে ন্যাকামি করে বাড়ি মাথায় করল—ওই লোককে আমি শ্বশুর করব। কখখনো নয়।”
অতুল বেশ চটে গিয়েছিল, কিন্তু অবস্থাটা যা তাতে পুরোপুরি ঝগড়া করাও যায় না। সে তো মেয়ে নয়, পুরুষ। তার খানিকটা সংযম ও কাণ্ডজ্ঞান থাকা দরকার। অতুল বলল, “আমার বাবা সম্পর্কে তুমি যা-তা বলছ! সত্তর বছরের বুড়ো আমার বাবা নয়। সিক্সটি ফাইভ সিক্স হবে। ন্যাকামি করার জন্যে কেউ স্লিপিং ট্যাবলেট খায় না…”
“ভীমরতি হলে খায়”, প্রীতি বেঁকা গলায় বলল।
“তোমার মা-ও কেরাসিন তেল খেয়েছিল”, পালটা ঠোক্কর দিল অতুল, “তোমার মা কচি খুকি নয়। বয়সটাও ষাটের কাছাকাছি। আমিও তো বলতে পারি তোমার মা ন্যাকামি করে কেরাসিন তেল খেয়েছিল।”
প্রীতি রুক্ষ গলায় বলল, “আমার মাকে তুমি ছেড়ে কথা বলছ নাকি? প্রথম থেকেই তো যা তা বলছ! …তুমি বলোনি, মার স্টমাক থেকে এখনও কেরাসিন তেলের গন্ধ উঠছে?”
অতুল আর এগুলো না ; হল্ট মেরে গেল। চেঁচামেচি ঝগড়া বচসা করে লাভ হবে না। অতুল বলল, “সরি! আমার অন্যায় হয়েছে! আসলে আমার মাথার ঠিক নেই। কটা দিন যা যাচ্ছে! কিন্তু তুমি এটা বুঝে দেখো, তোমার মা যদি আগে কেরাসিন তেল না খেত—আমার বাবা স্লিপিং ট্যাবলেট খেত না। এই কেলেঙ্কারির শুরু তোমার মা করেছে, আমার বাবা নয়।”
প্রীতি পিছিয়ে যাবার পাত্রী নয়। বলল, “আমার মা কেরাসিন খেয়েছিল তোমার বাবার জন্যে। তোমার বাবা দোতলায় খোলা বারান্দায় এসে আমার মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে গালাগাল দিত। বলত, ছেলেচোর ডাইনি, সর্বনাশিনী, আমার মার জিব নাকি মা কালীর মতন লকলক করছে। এসব কথা শুনলে কার মাথার ঠিক থাকে। আমার মা ছেলেচোর? তুমি কোন রাজপুত্তুর যে তোমাদের ওই ধ্যাড়-ধেড়ে দেড়খানা বাড়ির লোভে তোমায় চুরি করবে! নিজেকে তুমি রাজপুত্ত্বর ভাব নাকি? বেঁটে বাঁটকুল চেহারা, বিদ্যে তো বি. কম, চাকরি করো ব্যাঙ্কে—কেরানির। তোমার মতন রাজপুত্ত্বর এ-শহরে গড়াগড়ি যাচ্ছে। বেশি কথা বোলো না। ”
অতুল একেবারে স্তম্ভিত হয়ে প্রীতির দিকে তাকিয়ে থাকল। এ মেয়ে না রক্ষেকালী? জিবটা শান দিয়ে এসেছে নাকি প্রীতি? এতটা দেমাকই বা কিসের? তুমি কোথাকার রাজকুমারি গো? হাইট তো পাঁচ এক, মোটা হিলের জুতো পরলে ইঞ্চিখানেক বাড়ে। গায়ের রংটা একরকম ফরসা তা বলে তুমি সোনার বরণ নও। চ্যাপ্টা-ধ্যাবড়া চেহারা, ভোঁতা নাক, ছোট কপাল, খরখরে চোখ। নিজের চেহারাটা আয়নায় গিয়ে দেখো না সখি, দেমাক ভেঙে যাবে। লেখাপড়াতেই বা কী? কোনো রকমে টুকে-টাকে বি-এটা পাস করেছ।
অতুল মুখ ফিরিয়ে রেল লাইনের দিকে তাকাল। যেন এখন একটা মালগাড়ি থাকলে সে বোধহয় ঝাঁপ মেরে বসত।
একটু চুপচাপ। শেষ আলোটুকুও কখন আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে। মাসটা ভাদ্র। হয়তো শেষাশেষি। গাছপালা মাটির ভেজা-ভেজা গন্ধের সঙ্গে শরতের হাওয়া মিশে রয়েছে। আর সামান্য পরেই ঝাপসা অন্ধকার নামবে।
অতুলের বুকের মধ্যে মোচড় মারতে লাগল। একেই বলে জগৎ। সেই কবে—টুনি—যার কিনা পোশাকি নাম প্রীতি—সেই টুনির সঙ্গে তার সম্পর্ক। টুনি যখন ইজের পরত আর হরদম ইজেরের দড়িতে গিট লাগাত, গায়ে থাকত পেনি ফ্রক, মাথায় বব চুল—তখন থেকে টুনির সঙ্গে অতুলের গলাগলি সম্পর্ক। কতদিন টুনি অতুলকে দিয়ে ইজেরের দড়ির গিট খুলিয়ে নিয়েছে। সেসব দিনে টুনি যত ছেলেমানুষ ছিল অতুল অতটা ছিল না—টুনি পাঁচ, অতুল দশ—বছর পাঁচেকের ছোট বড়। সেই টুনি এখন একুশ, অতুল ছাব্বিশ। এত বছরের ভাব ভালবাসার পর টুনি আজ বলল, তুমি কোথাকার রাজপুত্তুর গো, ওই তো বেঁটে বাঁটকুল চেহারা, বিদ্যেতে বি. কম., ব্যাঙ্কের কেরানি…!
অতুল ডান হাতটা মাথার চুলে চিরুনির মতন করে চালিয়ে দিল। বুক হুহু করছে, এবং মনে হচ্ছে অসাড় রেল লাইনের মতন তার হৃদয়ট্রিদয়ও কেমন অসাড় হয়ে যাচ্ছে। গলার কাছটায় ফুলে উঠল অতুলের। কিন্তু এই রকমই হয়, এই তো জগৎ সংসার, প্রেম, ভালবাসা।
অতুল বেশ শব্দ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, “তা হলে আর কী! আমি যখন রাজপুত্তুর নই তখন এইখানে একটা শেষটেষ হয়ে যাক।”
প্রীতি এই সন্ধের মুখে কয়েকটা বককে সোঁ-সোঁ করে উড়ে যেতে দেখেছিল। এবং টেরা চোখে অতুলকেও। বলল, “করো না শেষটেষ, আমার কী। ”
অতুল মুখ উঁচু করে ওপারের প্ল্যাটফরমের দিকে তাকাল। বলল, “একুশটা বছর আমার নষ্ট হল। ওয়েস্ট…।”
“একুশ কেন?”
“তোমার পাঁচ ছ বছর থেকে ধরছি। আজ আমার ছাব্বিশ।”
“তুমি তোমার খুশি মতন ধরবে? আমার যখন পাঁচ-টাঁচ তখন আমি এখানে থাকতাম নাকি? মার সঙ্গে মামার বাড়িতে আসতাম-টাসতাম। আমি এখানে রয়েছি পাকাপাকিভাবে চোদ্দো পনেরো থেকে।” বলে প্রতি পিঠের বিনুনি বুকের ওপর টেনে নিল। বিনুনি নিয়ে কারুকর্ম করতে করতে বলল, “একুশ থেকে দশ বাদ দাও। তা হলে থাকছে এগারো। এগারো বছরের সম্পর্ক বলতে পারো…”
অতুল যদি পুরুষমানুষ না হত হয়ত কেঁদে ফেলত। মেয়েরা কি এই রকম নিষ্ঠুর হয়? ফ্রেইলিটি না কুয়েলিটি কোনটা মেয়েদের ঠিক ঠিক ভূষণ! কথার জবাব দিল না অতুল। আবার একটা সিগারেট ধরাল। টুনি যা বলেছে সেটা কোনো হিসেবই নয়। টুনি তো জন্মেছেই এখানে। তবু অতুল জন্মকাল থেকে ধরছে না। টুনির বাবা কাতরাসগড়ের লোক। সেখানেই থাকত টুনিরা। এখানে টুনির মামার বাড়ি। অতুলদের বাড়ির পাশেরটাই টুনিদের মামাবাড়ি ছিল। টুনির মাকে বরাবর পিসিমা বলে এসেছে অতুলরা। সেই পিসিমার বিয়েও দেখেছে অতুল—কিন্তু মনে নেই। টুনির জন্মও মনে পড়ে না ; কেননা অতুল তখন খুবই বাচ্চা ছিল। কিন্তু যখন থেকে মনে আছে তখন থেকে বাদ দেবে কেন? অতুল কি বলছে, টুনিরা এখানে বরাবর থাকত? না, অতুল সেকথা বলছে না। অতুল বলছে, ওই পাঁচ-টাঁচ থেকে—টুনির যখন পাঁচ অতুলের বছর দশ বয়েস—তখন থেকে সব তার মনে আছে। টুনি পিসিমার সঙ্গে মামার বাড়িতে আসত যেত, মাঝে মাঝেই আসত, ছুটি ছাটায় থাকত, আবার ফিরে যেত। একেবারে পাকাপাকিভাবে অবশ্য এল টুনির বাবা মারা যাবার পর। এখানে বাড়িতে ছিল টুনির দিদিমা। তিনি আগেই গিয়েছিলেন, টুনির মামা তখন বেঁচে, মামি মারা গেছেন, ছেলেপুলেও নেই, কাজেই পিসিমা আর টুনির বরাবরের জায়গা হয়ে গেল এবাড়িতে। সেই মামা—তিনিও বছর দুই হল মারা গেছেন। এখন টুনিরাই ওবাড়ির মালিক। বাডিতে লোেক জনও কম। নীচে এক ঘর ভাড়াটে আছে, ওপর তলায় থাকে টুনিরা।
সিগারেটে পর পর কয়েকটা টান মেরে অতুল বিমর্ষ গলায় বলল, “হিসেবটাকে তুমি আরও ছোট করতে পারো, আমি পারি না। মেয়েরা বরাবর কৃপণ। আমি তোমার মতন কিপ্টে হতে পারব না।”
প্রীতি ঘাড় বেঁকিয়ে বলল, “ছেলেরা হিসেব বাড়াতে পারে, তিলকে তাল করে—আমি তোমার মতন হিসেব বাড়াতে পারব না।”
“পেরো না।”
“পারব না। এগারো বছর ধরতে পারি।”
“ও-কে। সেই এগারো বছরের রিলেশান আজ শেষ হোক।”
“হোক। আমার কোনো আপত্তি নেই।”
“জানি-জানি। আমি তো রাজপুত্তুর নই। বেঁটে বাঁটকুল চেহারা, ব্যাঙ্কের কেরানি, বি কম। তুমি তো রাজকন্যে। হাঁটলে পায়ের নখ থেকে ইয়ে ঝরে পড়ে।”
প্রীতি কনুই দিয়ে খোঁচা মারল অতুলকে। অতুল কাতরে উঠল।
প্রীতি বলল, “চ্যাটাং চ্যাটাং কথা যদি বলবে, চিপটিনি কাটবে—তোমায় আমি শেষ করে দেব।”
“আমি কিছু অন্যায় বলিনি।”
“ন্যায় বলেছ।”
“হ্যাঁ।”
প্রীতি দু মুহূর্ত তাকিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। “তা হলে চলি!”
অতুল থতমত খেয়ে গেল। প্রীতি এইভাবে উঠে দাঁড়াবে সে ভাবতে পারেনি। বলল, “আমি তোমায় যেতে বলিনি।”
“তা হলে ন্যাকামি করছ কেন?”
অতুল আর কথা বাড়াতে ভরসা পাচ্ছিল না। বলল, “তোমার সঙ্গে কথা ছিল।”
“বলো।”
“দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হয় নাকি! বসো।”
“চাঅলা ডাকো।”
“এখানে চাঅলা কই?”
“ওদিকের প্ল্যাটফর্মে আছে। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকো।”
অগত্যা অতুলকে উঠতে হল, ওভারব্রিজের দিকে হেঁটে গেল খানিকটা। হাঁক পাড়ল বার কয়েক। টি স্টলের কেউ এদিকে আসবে মনে হল না। অতুলকেই লাফ মেরে রেল লাইনে নামতে হল, তারপর ওদিককার প্ল্যাটফর্মে উঠে পড়ল।
চা এনে প্রীতির হাতে দিচ্ছে যখন অতুল—তখন অন্ধকার হয়ে গেছে।
প্রীতি বসল না। পায়চারি করতে লাগল প্ল্যাটফর্মে। পাশে পাশে অতুলও। অতি মনোরম হাওয়া দিয়েছে তখন। তারা ফুটতে শুরু করেছে। প্রতি হাওয়ায় আঁচল উড়িয়ে পায়চারি করতে করতে গুনগুন করছিল।
অতুল বলল, “তুমি এত ফুর্তি পাচ্ছ কেমন করে আমি বুঝতে পারছি না।”
“একটা সিগারেট দাও না?”
“সিগারেট!”
“আরও ফুর্তি দেখাব।”
অতুল অবাক। এক আধবার সে নিজেই টুনির মুখে নিজের সিগারেট ঠেকিয়ে দিয়ে টানতে বলেছে, কেননা টুনি সিগারেটটা ঠোঁটে টিপে রাখতে পারে না, জিব লাগিয়ে ভিজিয়ে দেয়। অতুল যখন সেই সিগারেটটা আবার টেনে নিয়ে নিজের মুখে ঠোঁটে চেপে ধরে—অন্যরকম একটা স্বাদ লাগে তার, বেশ চনমন করে মনটা। কিন্তু আজ হল কি টুনির? সিগারেট ফুঁকতে চাইছে।
“তোমার যতই ফুর্তি হোক, আমার হচ্ছে না,” অতুল বলল, “আমি মরে আছি।”
“কেন?”
“কেন? তোমার মা—মানে পিসিমা খেল কেরাসিন তেল, আমার বাবা স্লিপিং ট্যাবলেট। পাড়ায় একটা কেচ্ছা হয়ে গেল। এরকম কেলেঙ্কারি আর কখনও হয়নি। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। পাড়ায় গিয়ে মুখ দেখাব কেমন করে?”
“আমি তো দেখাচ্ছি।”
“তোমার…” অতুল কোনো রকমে সামলে নিল। বলতে যাচ্ছিল—তোমার দু কান কাটা। সামলে নিয়ে বলল, “তোমার প্রচণ্ড সাহস। তা ছাড়া তুমি মেয়ে—যাবেই বা কোথায়! আমার মতন তো বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে বন্ধুদের মেসে গিয়ে থাকতে পারবে না।
“তুমি থাকছ কেন? কে বলেছে থাকতে?”
“বলাবলির দরকার করে না! যা কেচ্ছা হয়ে গেল—এরপর কোন ভদ্দরলোক বাড়িতে থাকতে পারে বলো—? আমার দাদাটি তো গিলে খাচ্ছে আমায়, বউদি মুখ বেঁকিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে বসে আছে।” অতুল সখেদে বলল। টান মারল সিগারেটে, তারপর আবার বলল, “সমস্ত কেলেঙ্কারিটা আমাদের নিয়ে। শালা বিয়ে করব আমরা, প্রেম করব আমরা। এটা আমাদের বিজনেস। তোমাদের কী? তোমার মা—মানে পিসিমার রাগ করে কেরাসিন তেল খাওয়াই বা কেন, আর আমার বাবার স্লিপিং ট্যাবলেট গিলে মরতে যাওয়াই বা কেন? লোকে বলে না, বুড়ো বয়সে ভীমরতি হয়, আমার বাবার তাই হয়েছে। এমনিতেই তো গলাবাজি করে সংসার কাঁপিয়ে রেখেছে তারপর ওই জেদ, জবরদস্তি। মরে যেতে ইচ্ছে করে, ভাই।”
প্রীতি হেসে ফেলল।
অতুল বলল, “হেসো না, হাসার ব্যাপার এটা নয়। আমার বাবা একটি ওয়ান্ডার। ছেলেকে জব্দ করতে কোনো বাপ ঘুমের ওষুধ খায়, শুনেছ?”
প্রীতি আরও জোরে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে নুয়ে গেল।
“হাসছ?” অতুল বলল।
“তোমায় জব্দ করতে না আমার মাকে জব্দ করতে?”
“পিসিমাকে জব্দ করতেও হতে পারে—তবে ওটা সেকেণ্ডারি। আমারটাই প্রাইমারি।”
প্রীতি অতুলের গায়ে ঠেলা মারল কাঁধ দিয়ে। বলল, “তুমি ঘোড়ার ডিম বুঝেছ! তোমার কোনো ব্যাপারই নেই।”
“নেই?”
“না মশাই, তোমার কেসই এটা নয়। মাকে নিয়েই সব ঝাট। মা রোজ রোজ তোমার বাবার—মানে মামার—এখন মামাই বলি—মামার হম্বিতম্বি, গালি-গালাজ, তড়পানি শুনতে শুনতে মনের দুঃখে কেরাসিন খেয়েছিল। পুরো বোতল খায়নি। আধ বোতল কি সিকি বোতল হতে পারে। আজকালকার কেরাসিনে যা জল, কতটুকু আর কেরাসিন পেটে গেছে—” বলতে বলতে প্রীতি ফট করে অতুলের মুখ থেকে সিগারেটটা টেনে নিল। নিয়ে নিজেই বার দুই টানল। টেনে থুথু করে ছুঁড়ে ফেলে দিল প্ল্যাটফর্মে।
অতুল ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাল ; কেউ যদি দেখে ফেলে। প্ল্যাটফর্ম ফাঁকা।
অতুল বলল, “পিসিমা কেরাসিন তেল খেয়েছে শুনেই বাবার ঘুমের বড়ি খাবার জেদ চেপে উঠল বলছ?”
“তা আর বলতে! …তুমি কেরাসিন তেল খেয়ে আমায় জব্দ করবে ভাবছ, দাঁড়াও আমি ঘুমের ওষুধ খাব…এই আরকি।” প্রীতি হাসছিল।
অতুল মাথা চুলকে বলল, “আমার একটা ডাউট আছে। বাবা মাত্র দুটো বড়ি খেয়ে ইয়ে হবে কেমন করে ভাবল? ঘুমের ওষুধ পেলই বা কোথায়?”
প্রীতি বলল, “ঘুমের ওষুধ না কচু, সোডার ট্যাবলেট খেয়েছে…কে আর দেখতে গেছে?”
অতুল জোর করে অস্বীকার করতে পারল না।
প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে পৌঁছে এবার ওরা ফিরতে লাগল।
অতুল বলল, “বাবার এই ছেলেমানুষির কোনো মানে হয় না। সমস্ত বাড়িতে একটা রই রই পড়িয়ে দিল। পাড়াময় রটে গেল, জনার্দনবাবু ঘুমের ওষুধ খেয়ে মরতে গিয়েছিল। স্ক্যান্ডেল!”
“আমার মা-টিও ওই রকম ; তবে তোমার বাবার মতন অতটা নয়!”
অতুল চুপ করে কয়েক পা হেঁটে এল। তারপর বলল, “দুজনের এই জেদাজিদি কেন আমি বুঝতে পারি না। কে কাকে জব্দ করবে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে নাকি?”
প্রীতি কিছুক্ষণ কথা বলল না, না বলে অতুলের বাঁ হাত নিজের ডান হাতে ধরে দোলাতে লাগল। যখন বেশ জোরে জোরে ওদের হাত দুলছিল—তখন আচমকা হেসে ফেলে প্রীতি বলল, “তুমি একেবারে কাঁচকলা। কিছু বোঝ না!”
“বুঝব কী! এর কিছু বোঝা যায় না।”
“যায় মশাই, যায়।”
“কী যায়?”
“বলব?”
“বলো!”
“তোমার বাবা লোকটি আমার মার সঙ্গে যৌবন বয়সে খুব প্রেম করত।”
অতুল প্রীতির হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে লাফ মেরে উঠল। বলল, “প্রেম—মানে বাবার ভাষায় প্রণয়।”
“আজ্ঞে হ্যাঁ, প্রণয়। পাশাপাশি বাড়ির ছেলেমেয়ে—ইয়ের বয়েস থেকেই প্রণয়। ”
“যাঃ যাঃ!”অতুল হাঁচির শব্দর মতন যা যা করল।
প্রীতি বলল, “মোটেই যাঃ যাঃ নয়। তোমার বাবা একটা ইয়ে—কোনো সাহস নেই, ভিতু, ডরপোক্কা। মার বিয়ে হয়ে গেল। তোমার বাবার আর তো কোনো ক্ষমতা হল না—মার ওপর রাগ নিয়ে বসে থাকল। সেই জের এখনও চলছে….”
অতুল সন্দেহের গলায় বলল, “আমার বাবা তোমার মার সঙ্গে প্রেম করত কে বলেছে?”
“দেখেছি” প্রীতি সটান গলায় বলল।
“তুমি দেখেছ?”
“হ্যাঁ মশাই দেখেছি। তোমার বাবার দেওয়া একটা বই মা এখনও কী যত্ন করে রেখে দিয়েছে। তাতে কি লেখা আছে জানো? লেখা আছে—আমার আদরের ধন লক্ষ্মীমণিকে।”
অতুল এবার সত্যি সত্যি লাফ মেরে উঠল। “যাঃ শালা। এই কেস। কী বই, মাইরি?”
“চন্দ্রশেখর। ”
“এই বইয়ের কথা তুমি আগে বলোনি তো?”
“আগে ছাই আমি দেখেছি নাকি। মা কোথায় লুকিয়ে রাখত কে জানে! বইটা তো সেদিন দেখলাম ; মার কেরাসিন তেল আর তোমার বাবার ঘুমের ওষুধ খাবার পর। মা এখন মাথার কাছে বইটা রেখে শুয়ে থাকে।”
অতুল বার কয়েক মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে নিল। ফস করে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর বলল, “আমার বাবাটা চরিত্রহীন নাকি?”
“চরিত্রহীন?”
“না তেমন চরিত্রহীন নয়। ক্যারেকটার নেই আর কি? প্রেম করতিস তো করতিস—সো হোয়াট? বিয়ে করলেই লেঠা চুকে যেত।”
প্রীতি জোরে চিমটি কাটল অতুলকে। তারপর জিব দেখাল। “ঘোড়ার মতন বুদ্ধি তোমার। তোমার বাবা আর আমার মা বিয়ে করলে—আমাদের কী হত মশাই? তোমায় যে দাদা বলতে হত!”
অতুলের খেয়াল হল যেন ব্যাপারটা। জিব কেটে ফেলল। বলল, “রিয়্যালি, আমার কোনো সেন্স নেই। খাজা মাথা। তুমি ঠিক বলছ! আমাদের ব্যাপারটার জন্যে ওদের স্যাক্রিফাইস করা উচিত ছিল। যাক গে, ওই বইটা আমাকে দিয়ো। ”
“কী করবে বই নিয়ে?”
অতুল রহস্যময় মুখ করে হাসল, ততোধিক রহস্যময় গলায় বলল, “ব্ল্যাকমেইল করব। প্রেশার দেব। তোমার আমার ব্যাপারে বাবা এবার যদি ঝামেলা করে—বইটা আমি আমার মার হাতে তুলে দেব। মা একটিবার শুধু দেখুক আমার ফাদারমশাই কাকে আদরের ধন ‘লক্ষ্মীমণি’ বলতেন। বাস ওতেই হয়ে যাবে। কিস্যু আর করতে হবে না আমাদের।”
প্রীতি একটুর জন্যে থমকে দাঁড়াল। তারপর দমকা হেসে উঠল। হাসি আর থামতেই চায় না। হাসতে হাসতেই বলল, “ভীষণ বুদ্ধি তো তোমার! এত বুদ্ধি ওই মাথায় ধরে রেখেছিলে! দেখি—দেখি—” বলে প্রীতি হাত বাড়িয়ে অতুলের চুলের ঝুঁটি ধরে মাথাটা নিজের মুখের কাছে নামিয়ে নিল। তারপর চকিতে একবার চারপাশ দেখে নিল প্ল্যাটফর্মের। কেউ নেই।
অতুল মুখ তুলে ভেজা গালের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে বলল, “বড্ড দাড়ি হয়ে গিয়েছে। স্কিনে টাচ করল না।”
দুজনেই হেসে উঠল একসঙ্গে। হাসতে হাসতে ওভারব্রিজের দিকে এগিয়ে চলল।
বৃদ্ধস্য ভার্যা
উমাশশী বারো হাত শাড়ি ধরেছেন সেই কোন যুগে—যখন তাঁর বয়স চল্লিশও হয়নি। এখন পঞ্চাশ চলছে। বারো হাতে আর কুলোয় না, যোলো হলেই যেন তাঁকে সবদিক থেকে মানাত। কিন্তু পাবেন কোথায়? দোকানে বাজারে বারো হাতই জোটে না সবসময়। এমনই বরাত উমাশশীর, পছন্দ মতন কোনো জিনিসই তাঁর ভাগ্যে এ-যাবৎ জুটল না। স্বামীও নয়।
অনেকটা বেলায় যখন কানাই এসে এক টুকরো কাগজ উমাশশীর হাতে তুলে দিল, কাগজের টুকরোয় বার দুই চোখ বুলিয়ে উমাশশী তাঁর বরাতের বহরটা দেখলেন। স্বামী গৃহত্যাগ করেছেন।
“আমি গৃহসংসার ত্যাগ করিলাম। বৃথা অন্বেষণ করিও না। তুমি তোমার সংসার লইয়া সুখে থাকো। ইহকালে আর সাক্ষাৎ হইবে না। পরকালেও যেন না হয়। ইতি সারদা গুপ্ত।”
“পুঃ : পথ খরচ হিসাবে কিছু লইয়া গেলাম।”
উমাশশী কচি খুকি নন, স্বামীর গৃহত্যাগের দৌড় তাঁর জানা আছে। বাষট্টি বছরের বুড়ো—যার এক গ্লাস জল গড়িয়ে খাবার ক্ষমতা নেই, দু পাটি দাঁতের অর্দ্ধেক বাঁধানো—সে করবে গৃহত্যাগ? ঢং কত!
ছোট মেয়েকেই ডাকলেন উমাশশী। ডেকে তাঁর শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। নিজে বেশি নড়াচড়া করতে পারেন না, ওঠা-বসা, কোমর নোয়ানো, উবু হওয়া—এসব তিনি প্রায় ত্যাগই করেছেন।
ঘরে এসে মেয়েকে বললেন, “আলমারি খোল, দেরাজ খোল। বাক্সটাজ যা আছে টেনে বার কর। দেখি তোর বাবা কী কী নিয়ে পালিয়েছে?”
মেয়ে মার কতটা বাধ্য বোঝা গেল না, বলল, “কোনটা আগে খুলব?”
“আলমারি।” আঁচল থেকে চাবিরর গোছা খুলে ঝনাৎ করে ফেলে দিলেন উমাশশী।
আলমারি, দেরাজ, কোণে রাখা ট্রাঙ্ক, ঘরের এ-কোন ও-কোন, তাক, খাটের তলা সমস্ত আঁতিপাঁতি খুঁজে মেয়ে—মানে আশা যখন গলদঘর্ম হয়ে উঠে দাঁড়াল তখন উমাশশী তাঁর প্রাথমিক তল্লাসি শেষ করে ফেলেছেন। ধোপা এবং সংসার খরচের খাতার একপাশে গোটা গোটা করে হারানো জিনিসের লিস্টি লেখা হয়ে গেছে।
তালিকাটা এইরকম ; নগদ টাকা চারশো ; একটি নবরত্ন আঙটি, একজোড়া ধুতি, একটি প্যান্ট, পায়জামা নতুন একটি, পাঞ্জাবি দুই, কর্তার বুশ শার্ট এক, গেঞ্জি দু’তিনটি, চাদর ও সোয়েটার একটি একটি, কর্তার দু’পাটি জুতো, এক শিশি মিল্ক অফ ম্যাগনেশিয়া, নতুন জবাকুসুম তেল ইত্যাদি।
ফর্দর দফা প্রায় এগারো হল। উমাশশী বুঝলেন, ঠিক যা যা বুড়োর লাগতে পারে—সবই নিয়ে পালিয়েছে। মায় একটা স্যুটকেস পর্যন্ত। পোস্ট অফিসের টাকা তোলার বই, ব্যাংকের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টের চেক খাতা, বাড়ির দলিলপত্রের কাগজ—এ-সব অবশ্য রেখেই গেছে। একটা জিনিস কিন্তু নিয়ে যেতে ভুলে গেছে, বুড়ো তারক কবিরাজের দেওয়া অর্শের ওষুধ। বুঝবে ঠেলা।
আশা তখনও হাঁফ সামলাচ্ছিল। বলল, “মা, বাবা কি সত্যি সত্যি রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে?”
উমাশশী বললেন, “রাগের মুখে আগুন। এঁচোড়ে পাকা বকাটে ছেলেদের মতন টাকা-পয়সা হাতিয়ে সোনাদানা চুরি করে পালাতে গেছে! লজ্জা করল না বুড়োর। যাবে যাও, ন্যাংটো ফকির হয়ে যাও। সংসারে যার অরুচি ধরেছে তার এত তল্পিতল্পা বাঁধা কেন?” জোরে কথা বললেই উমাশশীর গলায় কয়লার এঞ্জিনের ভোঁয়ের মতন সুর খেলে, বুক ধড়ফড় করে, ঘাম হয় মুখে। বুকে একবার হাত দিলেন তিনি। তিন ভরির বিছে হার গলায়। হারে আঙুল ঠেকতেই কেমন যেন সচেতন হয়ে হারটা দেখে নিলেন। এই হার সর্বক্ষণ তাঁর গলায় থাকে, হাতে তিন গাছা করে মোটা চুড়ি। চুড়িগুলো এমন করে বসে গেছে কজিতে যে ওগুলো খুলতে গেলেই উমাশশী জেগে যেতেন। খোলা অসম্ভব। তবে গলার হারটা খুলে নেওয়া যেত। সারদা গুপ্ত তা নেননি।
আশা বলল, “এখন কি করবে? দাদাকে খোঁজ নিতে পাঠাবে?”
উমাশশী মুখ বেঁকিয়ে বললেন, “কেন, খোঁজ করব কেন? বাষট্টি বছরের বুড়ো গিয়েছেন ঘরসংসার ত্যাগ করে নিমাইসন্ন্যাস হতে! যাক না! মজাটা বুঝুক। যার নেই কাছার ঠিক তার আবার গৃহত্যাগ। আবার লম্বা লম্বা কথা—ইহকালেও নয়, পরকালেও নয়—কোথাও নাকি দেখা হবে না। পরকালে আমি পেত্নি হয়ে তোমার ঘাড়ে চড়ে বসে থাকব—দেখি তুমি কেমন করে পালাও।”
আশা মুখ ফিরিয়ে জানলার দিকে তাকাল। মার মুখের দিকে তাকিয়ে একটুও যদি হেসে ফেলে, কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হয়ে যাবে।
“তোমার দাদা কোথায়?” উমাশশী জিজ্ঞেস করলেন।
“বেরিয়েছে কোথায় সাইকেল নিয়ে, আসবে এখুনি।”
“যেমন বাপ তার তেমনি ছেলে। সকাল থেকে ইয়ার বন্ধু করে বেড়াচ্ছে। একটা লোক বাড়ি ছেড়ে পালাল একরাশ জিনিস নিয়ে, তোমরা কেউ জানতেও পারলে না। বাড়িতে একটা কুকুর থাকলে সেটাও ঘেউ ঘেউ করত।”
আশা একেবারে থ। মার চোখে তারা কুকুরেরও অধম হয়ে গেল! একটু তাকিয়ে থাকল মার দিকে। রাগলে এখনও মার গালটাল টকটকে হয়ে ওঠে। চোখ দুটো ঝকঝক করছে। সাহস হল না আশার ; মনে মনে বলল, ‘তুমি তো পাশেই শুয়ে থাকো বাবার—তুমিই জানতে পেরেছ বাবা কখন পালিয়েছে।’
এ-সব সময় কথাটথা বলা উচিত নয়। আশা চুপ করেই থাকল, গোবেচারি অপরাধী মুখ করে ; যেন স্বীকার করে নিল—তারা দুই ভাইবোন একেবারে অপদার্থ, কুকুরের চেয়েও অধম।
উমাশশী রুক্ষ চোখে কিছুক্ষণ ঘরের এদিক ওদিক তাকিয়ে মেরের দিকে মুখ ফেরালেন। বললেন, “দাদা এলে বলো একবার থানায় যেতে হবে।”
“থানা?”
“থানায় গিয়ে ডায়েরি লেখাতে হবে। চুরির ফর্দটা আমি দিয়ে দেব।”
আশার মুখ আরও খানিকটা শুকিয়ে গেল। গলা পরিষ্কার করে বলল, “বাবার নামে থানায় ডায়েরি লেখাবে?”
“আলবত লেখাব। আমার বাড়ি থেকে জিনিস চুরি গেলে ডায়েরি লেখাব না? হাজার বার লেখাব। যা যা চুরি গিয়েছে—সব লেখাব”, উমাশশী তাঁর ফোলা ফোলা—পাকা কাঁঠালের কোয়ার মতন আঙুল তুলে শাসালেন, তারপর ডান হাতের তর্জনী বাঁ হাতের তালুতে ঠুকতে ঠুকতে বললেন, “থাকত আমার বাবা বেঁচে তো দেখে নিতাম। পালাত কোথায় তোমাদের গুপ্তবাবু? আমার বাবার হুকুমে ঘাড় ধরে টেনে আনত পুলিশ ওই নিমাইসন্ন্যাসকে। বুঝতে পারত—কত ধানে কত চাল।” উমাশশী হাঁফ ফেললেন, বুকটা ধড়ফড় করছে। বার দুই ঢোঁক গিলে বললেন, “পালানো অত সোজা। এ কি খরগোসের বাচ্চা নাকি যে দিলাম ছুট আর বনে গিয়ে লুকোলাম! তোমাদের বাবার কেরানি আমার জানা আছে। অনেক হম্বিতম্বি, পালাপালির চেষ্টা করেছে আগে। পেরেছে? আমার বাবার এক দাবড়ানিতেই সব ঠাণ্ডা।”
আশা ভয়ে ভয়ে বলল, “দাদু ছিল ডাকসাইটে পুলিশ অফিসার, দাদুর কথা আলাদা। এখানের এই ছোট্ট থানায় ডায়েরি লিখিয়ে তুমি কি করবে? ওরা কিছুই করতে পারবে না—শুধু শুধু লোক হাসাহাসি হবে।”
উমাশশী বললেন, “তোমায় কত্তামি করতে হবে না। আমি যা বলছি তাই হবে। তোমার দাদা এল কিনা দেখো! আর কানাইকে ডেকে দাও। আমি জানতে চাই—ওই চিরকুট সে কোথায় পেল।”
আশা আর দাঁড়াল না, পালিয়ে গেল।
উমাশশী বিছানার ওপর বসে থাকলে। মাথার দিকের জানলা খোলা, পায়ের দিকেরও। দু দিকের জানলাতেই ছোট ছোট পরদা, জানলার তলার দিকটা ঢাকা, ওপরটা ভোলা। মাথার জানলা দিয়ে বাইরের বাগান দেখা যায়, করবী আর কাঠচাঁপা, দু-একটা ঝাউ কিংবা জবাগাছ। বেশ রোদ পড়েছে বাগানে, ঝকঝক করছে। করবেই তো। এটা তো কার্তিক মাসের শেষ, কোথাও কোনো মেঘবাদলা নেই, সবই পরিষ্কার। বাগানে কাক চড়ই শালিখ ডাকাডাকি করছিল। উমাশশী কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। কার্তিক মাসে মানুষটা বাড়ি ছেড়ে পালাল। মাস বছর হিসেব করে না—এ কেমন লোক! আর ক’দিন পরেই অঘ্রাণ পড়ছে। বারোই অঘ্রাণ কর্তার জন্মদিন, তেষট্টি বছরে পড়বে। আর ঠিক এই সময়ে পালাল! বুড়ো হয়ে ভীমরতিতেই ধরেছে!
কানাই এসে দাঁড়াল নিচু মুখে।
“তুই ওই কাগজটা কোথায় পেয়েছিস?” উমাশশী ধমকের গলায় বললেন।
“বসার ঘরে”, কানাই বলল, “ঘরদোর ঝাট দিচ্ছিলাম, গোল টেবিলের ওপর থেকে পড়ে গেল।”
“টেবিলের ওপর থেকে এমনি এমনি কাগজ পড়ে যায়?” উমাশশী সন্দেহের গলায় বললেন।
কানাই থতমত খেয়ে বলল, “টেবিল সরিয়ে রাখছিলাম, মা।”
“কখন ঘুম থেকে উঠেছিস?”
“আজ্ঞে, ভোর কালে।”
“বাবু ভোরবেলায় ওঠেন, হাঁটাহাঁটি করেন—বাবুকে দেখিসনি?”
“না, মা।”
“না, মা! তুই ভোরবেলায় উঠিসনি? খাস কি রাত্তিরে? গাঁজা? গাঁজাখোরের মতনই তো চেহারা করেছিস! যতসব আমার কপালে জোটে। সব কটাকে তাড়িয়ে দেব একদিন। বাড়িতে চুরি ডাকাতি হয়ে গেলেও তোরা কুম্ভকর্ণের ঘুম ঘুমোবি!…কামিনীকে ডাক। তিনি তো রান্নাঘরে বসে বসে পান-জরদাই খেতে শিখেছেন।”
কানাই এ-বাড়ির পুরনো লোক। গিন্নিমার মতিগতি বোঝে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সরে গেল উমাশশীর চোখের সামনে থেকে।
উমাশশীর মাথা গরম হয়ে উঠেছে। মাথা গরম হলেই কপালের শিরা দপদপ করে। মাথার পেছনদিকে ঘাড় বরাবর ব্যথা হয় কেমন। গোপী ডাক্তারকে ডাকলেই ব্লাডপ্রেশার যন্ত্র বার করে বসে, একটা পট্টি বেঁধে দেয় হাতে, কানে তার স্টেথস্কোপের নল গোঁজে ; কি যে দেখে ছাই কে জানে! বলে, হাই। খাওয়া দাওয়ার ধরাকাটা করুন, আলুটালু খাবেন না, নুন না হলেই ভাল, এটা করবেন না ওটা করবেন না। নিকুচি করেছে তার ডাক্তারির! কিছুই করব না তো সংসারে রয়েছি কেন, চিতায় গিয়ে শুয়ে পড়লেই হয়।
কামিনী এল।
কামিনীর দিকে চোখ পড়তেই উমাশশী ঝাঁঝালো গলায় বললেন, “করছিলে কী তুমি?”
কামিনী বলল, “উনুনে আঁচ পড়ে যাচ্ছিল, ঝামা কয়লা। আঁচ তুলে কুটনো কুটতে বসেছিলাম।”
“আমার মাথা কুটতে বসেছিলে,—“ উমাশশী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, “পান সাজতে আর গালে পুরতে তোমার দিন চলে যায়। একগোছ করে পান আসে রোজ, কে অত পান খায়?”
কামিনী চুপ করে থাকল, একগোছ পানের প্রায় সবটাই যে গিন্নিমার মুখে যায়—এই সত্যি কথাটা তার বলার সাহস হল না। পান জরদার নেশা নিয়ে কামিনী এ-বাড়িতে কাজে ঢোকেনি, গিন্নিমার পান সেজে দিতে দিতে তারও নেশা ধরেছে।
“সকালে যখন ঘরদোরের তালা খুলে ঝাটপাট দিচ্ছিলে হেঁসেলের দিকে—বাবুর গলাটলা পাওনি?”
“না, মা।”
“সকালে বাবুর চা করোনি?”
“করেছি। চা নিয়ে বসার ঘরে গিয়ে দেখি বাবু নেই। বারান্দাতেও ছিলেন না। বাগানেও দেখিনি বাবুকে।”
“দেখতে পেলে না তো আমায় ডাকলে না কেন?”
কামিনী চুপ করেই থাকল ; সকালে বাবুকে চা দিতে গিয়ে দেখতে না পেলে যে গিন্নিমার শোবার ঘরে গিয়ে তাঁর ঘুম ভাঙাতে হবে—কামিনীর তা জানা ছিল না। এই প্রথম জানল।
কত যেন অপরাধ হয়ে গেছে, কামিনী একটু চুপ করে থেকে মিনমিনে গলায় বলল, “বাবুকে সকাল থেকেই দেখছি না, মা! কোথায় গিয়েছেন তিনি?”
উমাশশী করকরে চোখে তাকালেন কামিনীর দিকে। সমস্ত মুখে বিরক্তি। কপাল ভুরু কুঁচকে রয়েছে। বললেন, “জানি না। গিয়েছেন কোথাও।…তুমি নিজের কাজে যাও। একটু জল দিয়ে যেও।”
কামিনী চলে গেল।
উমাশশী চুপচাপ বসেই থাকলেন বিছানায়। এ রকম অবস্থা তাঁর কখনো হয়নি। মানুষটা তাঁকে একেবারে বোকা বানিয়ে পালিয়ে গেল। পাশাপাশি বিছানায় শুয়ে থাকেন দুজনে, ওরই মধ্যে কখন যে ও উঠল, জিনিসপত্র গোছাল, আলমারি দেরাজ খুলল—টাকাপয়সা আংটি হাতাল, তারপর চুপিচুপি পালিয়ে গেল—উমাশশী কিছুই বুঝতে পারলেন না। তাঁকে কি কালঘুমে পেয়েছিল? নাকি ওই বুড়ো তাঁকে চোর ডাকাতদের মতন বেঁহুশ করে রেখে কাজ গুছিয়ে পালিয়ে গেছেন।
প্রথম রাতের দিকে উমাশশীর ভাল ঘুম আসে না। হাঁটু, পায়ের গোছ, হাতের গাঁট—কোথায় না বাতের ব্যথা! তার ওপর মাথা গরমের ধাত, বুকেরও ধড়ফড়ানি রয়েছে। আজকাল দু-একদিন অন্তর ঘুমের বড়িও খেতে হয় এক আধটা। কালও খেয়েছিলেন। কিন্তু তাতে মড়ার ঘুম কেন ঘুমোবেন?
প্রথম রাতের দিকে উমাশশী একরকম জেগেই থাকেন, মাঝরাত নাগাদ ঘুমিয়ে পড়েন। ভোরের দিকে উঠতে পারেন না। খানিকটা বেলা হয় ঘুম ভাঙতে। ঘুম ভাঙলে ঠাকুর নাম জপতে জপতে যান চোখেমুখে জল দিয়ে আসতে। কামিনী চা দেয়। চা খেয়ে দু-চারটে ছোটখাটো কাজ সেরে চলে যান স্নানে। স্নানের ঘর থেকে সোজা ঠাকুরঘরে। পুজোআর্চা সেরে নিজের ঘরে আসেন। গরদের শাড়ি ছেড়ে জামাকাপড় বদলে সংসারের কাজেকর্মে হাত দেন। এই সময়টায়—যতক্ষণ না তিনি সংসারের কাজে এসে হাত দিচ্ছেন—তাঁকে কেউ কিছু বলে না। বললেই সর্বনাশ। আজকেও উমাশশী ব্যাপারটা জানতে পারলেন অনেক পরে। কর্তা বাড়িতে নেই—এটা তাঁর কানে গিয়েছিল পুজোর ঘর থেকে বেরিয়েই। তাঁর কোনো কিছু মনে হয়নি, সন্দেহও নয়। কর্তা প্রায় সকালের দিকে স্টেশনের দিকে যান গল্পগুজব করতে, নন্দীমশাইয়ের বাড়ি যান আড্ডা দিতে, একটু আধটু বাজারটাজার ঘুরে আসেন, পোস্ট অফিসেও ঢুঁ মারেন।…মানুষটা বাড়িতে নেই বলে যে পালিয়ে যাবে এটা উমাশশী কেমন করে বুঝবেন?
বুঝলেন আরও খানিকটা পরে, কানাই যখন চিরকুটটা এনে দিল। পড়ে বিশ্বাস করতে পারেননি ; তারপর যখন দেখলেন ঘর থেকে নগদ টাকা, আংটি, জামাকাপড়, স্যুটকেস—সবই উধাও তখন বুঝলেন, মানুষটা পালিয়েছে।
কিন্তু পালাল কেন? কাল তো তেমন কোনো ঝগড়াঝাটি হয়নি। সকালে কর্তার মেজাজ খুব ভাল ছিল। উমাশশী ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে যখন শোবার ঘরে এলেন কাপড় চোপড় ছাড়তে কত তখন ঘরে, ওই জানলার সামনে বসে সিগারেট ফুঁকছেন। এখন আর লজ্জা শরমের বয়েস নেই, উমাশশী ঘরের একপাশে দাঁড়িয়ে জামা-কাপড় পরতে পরতে শুনলেন কর্তা একটু খাটো গলায় মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে ফক্কুড়ির সুরে ‘গীতগোবিন্দ’-র গান ধরেছেন। ওই জিনিসটি ওঁর দখলে আছে। গান গাইতে গাইতে উঠে এসে কর্তা উমাশশীর গায়ের কাপড় ধরে টান মারলেন—‘বিগলিত-বসনং পরিহৃত-রসনং’ আরও কি কি ‘পয়োধর-ভার-ভরেণ’ বলতে বলতে সাত সকালে গাল চাটার জন্যে মুখ বাড়াতেই এক ঠেলায় কর্তাকে দশ পা হটিয়ে দিলেন উমাশশী। বুড়ো বয়েসে ঢংয়ের শেষ নেই। কর্তা এতেই চটে গেলেন। বয়েই গেল উমাশশীর। এরপর আর কিছু ঘটেনি। ভাতের পাতে বরাবরই খানিকটা ঘন দুধ খান কর্তার। বয়েস তো হয়েছে। দুধের জ্বাল ভাল হয়নি। রাগারাগি করছিলেন। তা উমাশশী তখন দু’কথা বলেছিলেন। বিকেলও কোনো অশান্তি হয়নি। সন্ধেবেলায় আবার একপশলা হয়েছিল, সেটাও তেমন কিছু নয়। রাত্রে বাক্যালাপই হয়নি। তা হলে মানুষটা পালাবে কেন?
কামিনী পান, জল নিয়ে এল।
উমাশশী জল খেলেন। পান জরদা মুখে পুরলেন। তারপর পাখাটা খুলে দিতে বললেন—গরম লাগছিল।
কামিনী চলে যাবার পর উমাশশী স্থির করলেন, বড় মেয়ে এবং ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজনদের চিঠি পাঠাতে হবে। নিজে লিখবেন না, মেয়ে কিংবা ছেলেকে দিয়ে লেখবেন। কোথাও গিয়ে দু’দিন গা ঢাকা দিয়ে উমাশশীকে জব্দ করবার চেষ্টা করছে বুড়ো। উমাশশী জব্দ হবার মানুষ কিনা! জব্দ তুমিই হবে। দু’দিনেই তোমার তেল শুকোবে। সাতকাল গিয়ে এককালে ঠেকল—এখন উনি হবেন নিমাইসন্ন্যাস! চোর জোচ্চোরের মুখে বড় বড় কথা!
উমাশশী জোরে জোরেই বললেন, “দেখব তোমার মুরোদ, করো না গৃহত্যাগ। তোমার ত্যাগ আমার জানা আছে।”
দিন দুই পরে আশা এসে মাকে বলল, “বাবার চিঠি এসেছে।”
উমাশশী জানতেন, আসবে। টিকি তো এখানেই বাঁধা ; যাবে কোথায়? ধরুক না একবার অর্শ। তখন তারক কবিরাজের মলম আর উমাশশীর তোয়াজ ছাড়া চলবে না। ডুকরে কাঁদতে হবে। বিজয়িনীর মুখ করে উমাশশী বললেন, “কই চিঠি?”
আশা মিনমিনে গলায় বলল, “দাদাকে লিখেছে।”
উমাশশী গ্রাহ্য করলেন না! মুখ আছে না সাহস আছে ওই গুপ্তবাবুর যে স্ত্রীকে চিঠি লিখবে। ছেলেমেয়েকেই লিখতে হবে, ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদুনিটা ওই ভাবেই গাইতে হবে এখন।
“দাদাকে ডাক।”
“আসতে চাইছে না।”
“ওর ঘাড় আসবে।”
আশা দাদাকে ডাকতে গেল।
উমাশশী অপেক্ষা করতে লাগলেন ছেলের।
তপন এল, সঙ্গে আশা।
“কখন এল চিঠি?” উমাশশী ছেলেকে দেখামাত্র জিজ্ঞেস করলেন।
“এই তো পিয়ন দিয়ে গেল”, তপন বলল।
“কোথায় গিয়ে বসে আছে?” পচুঠাকুরপোর কাছে না মণির কাছে?”
তপন চোরের মতনই এসেছিল ; দাঁড়িয়ে থাকল চোরের মতন। হাতে একটা খাম। মার দিকে ভাল করে চোখ তুলে তাকাচ্ছিল না। আশা ঠিক তার পেছনে।
“ঠিকানা লেখেনি”, তখন ঢোঁক গিলে বলল।
উমাশশী ছেলেকে ভুরু কুঁচকে দেখছিলেন। বাপের নখের যুগ্যিও নয় ছেলে। জোয়ান মদ্দ ছোঁড়া অথচ বাপের মতন লম্বা চওড়া কাঠামো নেই, বেঁটে লিকলিকে চেহারা, মাথায় রাজ্যের চুল, একেবারে মেয়ে-মেয়ে গড়ন পেটন।
“ঠিকানা দেবে না তো লিখবে কেন চিঠি?” উমাশশী ধমকে উঠলেন। “কী লিখেছে তোমার বাবা?”
তপন একবার মার দিকে চোখ তুলেই নামিয়ে নিল। চট করে দেখে নিল আশাকে। তারপর খামটা এগিয়ে দিল মার দিকে।
উমাশশী হাত বাড়িয়েই রেখেছিলেন। নিয়ে নিলেন চিঠিটা। খামের মুখ ছেঁড়া। ছেলেমেয়ে আগেই পড়েছে।
আশা তৈরি ছিল। চশমাটা এনে দিল দেরাজের ওপর থেকে।
চোখে চশমা আঁটলে উমাশশীকে আরও গম্ভীর গম্ভীর দেখায়। চশমা পরে চিঠিটা বার করলেন উমাশশী। মাথার দিকে কোনো ঠিকানা নেই।
চিঠিটা পড়তে লাগলেন:
“কল্যাণবরেষু,
তপু, আমি যে গৃহত্যাগ করিয়াছি, আশা করি তোমরা এতদিনে তাহা সুনিশ্চিতভাবেই বুঝিতে পারিয়াছ। যাহা ত্যাগ করিয়াছি তাহা আর গ্রহণ করিবার বাসনা আমার ইহজীবনে নই। আমি আর গৃহে ফিরিব না। গৃহের সুখশান্তি আমার বিলক্ষণ জানা হইয়া গিয়াছে। ত্রিশ বত্রিশ বৎসর গৃহসংসার করিলাম ; একটি কাঁঠালবিচি মাটিতে পুঁতিলে বত্রিশ বৎসরে বিরাট কাঁঠালবৃক্ষ হইয়া যায়, আর আমার ত্রিশ বৎসর বয়েসে তোমাদের দাদামহাশয় (তোমাদের গর্ভধারিণীর পিতা) যে বিচিটি আমার জীবনে পুঁতিয়া দিয়াছিলেন তাহাতে এই বত্রিশ বৎসরে আমার জীবনটি যে কীরূপ ফলময় হইয়া গিয়াছে তাহা তোমরা বুঝিবে না। কিছুটা বা অনুমান করিতেও পার। তোমরা আমার স্নেহের সন্তান। তোমাদের জন্যই দুঃখ হয়। তোমার দিদির বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সে বাঁচিয়াছে। তোমার বোনের বিবাহ আজ অথবা কাল হইয়া যাইবে, সেও বাঁচিবে। তোমার গতি কী হইবে? তোমার জন্যই দুশ্চিন্তা।
আমি স্থির করিয়াছি—তোমাকে আমি মাঝে মাঝে পত্র দিব। উত্তর আশা করি না, কারণ আমার ঠিকানা তোমায় দিব না। দিবার উপায়ও নাই। কোথায় থাকিব বলিতে পারি না। এই যে পত্রটি লিখিতেছি—কোথা হইতে লিখিতেছি বলিতে পার? একটি মনোরম ধর্মশালা হইতে। ইহা সাধুসজ্জনের স্থান। শান্ত, নিরিবিলি ধর্মশালা। নিকটেই গঙ্গানদী। হু-হু করিয়া বাতাস আসিতেছে, জটাজূটধারী এক সন্ন্যাসী জলদকণ্ঠে গীত গাহিতেছে। আহা, কী সুন্দর।
আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে, তুমি আমার একটিমাত্র পুত্র। তোমায় কিছু উপদেশ দেওয়া আমার কর্তব্য। সেই মতো আমি তোমায় পত্র লিখিব। আশাকেও পত্রগুলি পড়াইতে পার। তোমার মাতাঠাকুরানীকে না পড়াইলেই ভাল। কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে কিছু লুকাইবার ক্ষমতা তোমাদের নাই। তাঁহাকেও পড়াইবে। আমি আর তাঁহাকে ডরাই না। তিনি আমার গ্রিনব্যানানা করিবেন।
তোমার প্রতি আমার প্রথম উপদেশ, কখনো পুলিশের মেয়েকে বিবাহ করিবে না। পুলিশের মেয়েকে বিবাহ করিয়া আমি সারা জীবন নষ্ট করিলাম। পুলিশের মেয়েকে যদি বিবাহ কর জানিবে তোমার সমস্ত স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ইহারা জামাইষষ্ঠিতেও আসামী ধরার মতন করিয়া নিজেদের জামাইকে ধরিয়া আনে। আমি ভুক্তভোগী। একবার নয়, অন্তত তিনবার আমার শ্বশুরমহাশয়—যিনি বিহার গভর্নমেন্টের এস. পি. জি. ছিলেন—আমাকে দুইবার মুঙ্গের হইতে, আর একবার ভাগলপুর হইতে একজোড়া কনস্টেবল পাঠাইয়া ধরিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ অত্যাচারের আরও নমুনা পরে দিব। তবে জানিয়া রাখো আমার অমন পিতৃদত্ত নামটি সারদাপ্রসাদ গুপ্ত, সংক্ষেপে যাহাকে এস. পি. বলে, তাহা আমার কাছে চরম ব্যঙ্গের মতন শুনাইত। বন্ধুরা বলিতেন—এস. পি. জি. অর্থে ‘এস পি’র গোট।
তুমি মানুষ, ছাগল নও। পুলিশের মেয়ে বিবাহ করিলে তোমায় ছাগল হইয়া থাকিতে হইবে। আমার প্রথম উপদেশটি আজ তোমায় দিলাম। অবশ্য তুমি এখনও তেমন সাবালক নও। তোমার বিবাহেরও যথেষ্ট বিলম্ব আছে। তথাপি এখন হইতেই জানিয়া রাখা ভাল।
আমার লণ্ঠনের শিখাটি মিটিমিটি করিতেছে। বোধ হয় তৈল নাই। অদ্যকার মতন শেষ করিতেছি। আমি চমৎকার আছি। শরীর স্বাস্থ্য ভাল। গব্যঘৃত সহযোগে আতপচালের ভাত খাইতেছি। সুস্বাদু দুধ। ধর্মশালার ঘরটিও চমৎকার। গঙ্গার বাতাস, মুক্ত আকাশ, একটি কম্বলের বিছানা আর সাধুসজ্জনের সঙ্গ—ইহার অপেক্ষা আনন্দের কী আছে!
তোমার গর্ভধারিণী মহাতেজস্বিনী মাতাকে বলিবে—আমি বাঁচিয়া আছি, তিনি যেন সধবার আহার-বিহার করিয়া সুখে থাকেন। তোমরা আমার আশীর্বাদ লইবে। ইতি আশীর্বাদক, তোমাদের বাবা।”
চিঠিটা পড়ার সময় উমাশশীর মুখের ভাব কতবার পালটে যাচ্ছিল ছেলেমেয়েরা তা নজর করার সাহস করল না। তপন দাঁড়িয়ে থাকল—ভাবটা এমন যে, তার কোনো দোষ নেই, বাবা এরকম চিঠি লিখবে সে কেমন করে বুঝবে। এই জন্যেই তো সে চিঠি নিয়ে আসতে চাইছিল না।
চিঠিটা শেষ করে উমাশশী আগুনের ঝলকের মতন চোখ করে ছেলেমেয়ের দিকে তাকালে। চোখমুখ টকটক করছে। টান মেরে ফেলে দিলেন কাগজটা, তারপর চেঁচিয়ে বললেন, “পুলিশের মেয়ে বিয়ে করে উনি ছাগল হয়েছিলেন! আচ্ছা, ঠিক আছে। এখন তো উনি সিংহ। ধর্মশালার আতপ আর ঘি খেয়ে গর্জন করছেন। আমিও দেখব।”
দুটো সপ্তাহ দেখতে দেখতে কেটে গেল। উমাশশী আশা করেছিলেন, হাতের নগদ টাকা ফুরোলেই কর্তাকে ফিরতে হবে। যেরকম কাছাখোলা, বেহিসেবি মানুষ তাতে চারশো টাকার তেজ বেশিদিন থাকবে না। অবশ্য যাবার সময় নবরত্নের আংটিটা চুরি করে নিয়ে গেছে ও। আংটির মালিক আংটি নিয়েছে তাতে কিছু নয় ; কিন্তু টান পড়লে সেটাও কি বেচে দেবে?
ছেলেমেয়েদের দিয়ে উমাশশী চিঠি লিখিয়েছেন সাত আট জায়গায় : কলকাতায়, পাটনায়, টাটানগরে, মিরজাপুরে, বেনারসে প্রায় সব জায়গাতেই—যেখানে কোনো কোনো ঘনিষ্ঠ আত্মীয়স্বজন রয়েছে। একেবারে নিজের বলতে কর্তার কেউ নেই, উমাশশীরও নয়—এক বড় মেয়ে ছাড়া। খুড়তুতো জ্যাঠতুতো মাসতুতো ভাই বোনরাই যা রয়েছে দু’তরফের। আজকাল চিঠিপত্রেই যা যোগাযোগ, আগে মাঝে মাঝে তারা আসত-টাসত, এখন আর সে সময় কই, সুযোগই বা কোথায়!
উমাশশী কচি খুকি নন, তাঁর বোধবুদ্ধি যথেষ্ট। লোক হাসানোর কাজ তিনি করবেন না। ছেলেমেয়েদের বলে দিয়েছিলেন, “তোমাদের বাবা বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছেন এ সব কথা কিছু লিখো না। লোকে হাসবে। তোমাদের বাবার তাতে মান বাড়বে না। গুণের তো শেষ নেই বাবুর। সবাই জানে। ঘর ছেড়ে পালানোর কথা লিখবে না ; একথা ওকথার পর শুধু লিখবে—তোমাদের বাবা এখন এখানে নেই, বাইরে গেছেন। ওতেই কাজ হবে। কোথাও যদি গিয়ে উঠে থাকেন তোমাদের বাবা ওদের জবাবে জানতে পারব। তোমাদের দিদিকেও ওইরকম লিখবে। তার শ্বশুরবাড়িতে দিদির মানসম্মান আছে। তার বাবা বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে—এটা জামাইয়ের জানার দরকার নেই, তাতে তো তোমাদের মুখ উজ্জ্বল হবে না।”
ছেলেমেয়েরা চিঠি লিখে লিখে মাকে দেখিয়েছিল ; উমাশশী সব চিঠি আগাগোড়া পড়ে নিজের হাতে খামের মুখ এঁটে দিয়েছিলেন।
এই পনেরো দিনে অনেকের চিঠিরই জবাব এল, কিন্তু কেউ লিখল না কর্তার কারও কাছে গিয়ে উঠেছেন।
উমাশশী ভাঙবার পাত্রী নন, গুপ্তবাবুকে হাড়ে হাড়ে চেনেন। সারা জীবন ধরে জ্বলছেন উমাশশী ; অনেক রাগ অভিমান তর্জন গর্জন দেখেছেন ; গুপ্তবাবু হলেন গাদা বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ, আওয়াজ ছাড়া তাঁর কিছু নেই। কিন্তু নিজেকে যতই সামলান, থেকে থেকে মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। গেল কোথায় মানুষটা?
ছেলেমেয়ের কাছে ইতিমধ্যে আরও তিন চারটে চিঠি এসেছে কর্তার ; উমাশশী দেখেছেন। তাঁর বড় অবাক লাগে। চিঠিতে কোনো ঠিকানা নেই—। সে না হয় কর্তা না দিলেন, কিন্তু খামের ওপর পোস্ট অফিসের ছাপ দেখেও কিছু বোঝার উপায় নেই। এমনই ছাপ যে একটা অক্ষরও পড়া যায় না। চিঠিগুলো কোথা থেকে আসে বোঝা গেলেও না হয় উমাশশী ধরতে পারতেন কর্তার গতিবিধি কোন দিকে।
সেদিনও একটা চিঠি এল ছেলের নামে। যথারীতি উমাশশীকে দেখানো হল। উমাশশী দেখলেন, পড়লেন ; কিছু বললেন না। গুপ্তবাবু একতরফা চালাচ্ছেন, প্রত্যেকটি চিঠিতে উমাশশীর মুণ্ডপাত করছেন, খোঁচার ওপর খোঁচা, চিমটে গরম করে গায়ে ছেঁকা দিলেও এত লাগত না। এক একসময় উমাশশীর মনে হয়, তাঁর গায়ের চামড়া কেটে কেটে লেবুর রস আর নুন ছড়িয়ে গুপ্তবাবু যেন জ্বালাটা দেখবার চেষ্টা করছেন। কোনো উপায় নেই উমাশশীর, আড়াল থেকে যে-লোক লড়াই চালায় তাকে মানুষ ধরবে কেমন করে? সামনাসামনি হলে দেখে নিতেন তিনি। কাপুরুষ কোথাকার! সাহস নেই যে সামনে দাঁড়িয়ে লড়বে, আড়ালে গিয়ে উমাশশীকে চোরা বাণ মারছ, ভাবছ তাতে তোমার পৌরুষ বাড়ছে। ঘেন্না ধরে গেল তোমায় দেখে।
এক একদিন এই বয়েসেও চোখে জল চলে আসে উমাশশীর। বাবা বেঁচে থাকলে একবার দেখতেন সারদা গুপ্তকে, কোমরে দড়ি বাঁধিয়ে ধরিয়ে আনাতেন। আজ বাবা নেই, উমাশশী একেবারে অসহায়। এমনই কপাল তাঁর, নিজের পেটের ছেলেমেয়ে দুটোকেও নষ্ট করে দিচ্ছে তাদের বাপ, মার নামে লাগিয়ে লাগিয়ে একেবারে যাচ্ছেতাই কাণ্ড করছে। উমাশশী তো বলতে পারেন না, তোদের বাবার চিঠি তোরা পড়বি না—আমায় এনে দিবি—আমি আগুনে ফেলে দেব।’ ছেলেমেয়েরা শুনবে কেন? হয়তো দেখা যাবে, বাপের চিঠির কথা আর তারা মার কাছে জানাচ্ছে না। লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ছে। এ তবু বোঝা যায়, চিঠিপত্তর এলে, মানুষটা কোথাও না কোথাও রয়েছে ; ছেলেমেয়েরা যদি চিঠির কথা লুকোয় উমাশশী কিছুই জানতে পারবেন না।
শরীরটা দুপুর থেকেই ভাল ছিল না। পূর্ণিমা সামনে। কোমরে, হাঁটুতে, আঙুলের গাঁটে বাতের টনটনানি। বিকেলের দিকে উমাশশী বাইরের বারান্দায় বসেছিলেন খানিক। তাড়াতাড়ি বেলা পড়ে যাচ্ছে আজকাল। সন্ধের মুখে বিকেলের কাপড় চোপড় ছেড়ে সোজা ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।
শুয়ে থাকতে থাকতে মনটা বড় মুষড়ে পড়ল। জোড়া খাটের একটা আজ কতদিন ধরে ফাঁকা, বড় বড় বালিশগুলো টানটান হয়ে পড়ে থাকে, মাথার দাগ পড়ে না কোথাও। বিছানার চাদর-টাদরও একবিন্দু কোঁচকায় না। ঘরের কোণে আলনায় কর্তার একটা ময়লা পাজামার পা দু’টো ঝুলছে। যেন আড়ালে বসে ভূতের মতন গা দোলাচ্ছেন কর্তা। কর্তা ঘরে থাকলে তামাকের গন্ধ থাকে—কাগজ পাকিয়ে সিগারেট খান—সেই গন্ধও আর নেই। পায়ের চটি দুটো বরাবরই খাটের তলায় পড়ে থাকত ; তাও নেই।
বেশ ফাঁকাই লাগে আজকাল উমাশশীর ঘরটা। মেয়ে এসে শুতে চেয়েছিল রাত্তিরে ; উমাশশী না করে দিয়েছেন। তার বিছানায় কেউ কোনোদিন শোয়নি, কাউকে শুতে দেননি উমাশশী, ছেলেমেয়েরা যখন কচি ছিল তখনও নিজের বিছানায় রেখেছেন, তারপর আজ কতকাল তো দুই বুড়োবুড়ি এইভাবে শুয়ে এলেন। থাক, পড়ে থাক ফাকা বিছানা, উমাশশী নিজের ঘরে একাই শুতে পারবেন।
মনটা ভাল ছিল না। পাঁচ রকম ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তাঁর কী খেয়াল হল, কানাইকে ডাকলেন। কানাই এলে বললেন, “দিদিকে একবার ডেকে দে। কামিনীকে বল, আমায় একটু চা দিয়ে যাবে, আর পান।”
কানাই চলে গেল ; একটু পরেই আশা এসে দাঁড়াল।
উমাশশী বললেন, “তোমার বাবার চিঠিগুলো রেখেছ, না ফেলে দিয়েছ?”
“আছে।”
“চিঠিগুলো আমায় এনে দাও। সমস্ত চিঠি। খামগুলো আছে না গেছে?”
“রয়েছে।”
“ওগুলোও আনবে। …দাদা কোথায়?”
“এই তো বাড়ি ফিরল।”
“জানলার দিকের বাতিটা নিবিয়ে মাথার দিকেরটা জ্বেলে দাও। আমার চশমাটাও দিয়ে যাবে।”
মা’র হুকুম মতন আশা একদিকের বাতি নেবাল, মাথার দিকেরটা জ্বালল। চশমা এনে দিল। তারপর চিঠিগুলো আনতে চলে গেল ঘর ছেড়ে।
আশা সামান্য পরেই ফিরে এল চিঠি নিয়ে। কামিনীর দেরি হল আসতে। চা এনেছে, পানের ডিবে আর জরদার কৌটো।
উমাশশী ধীরে সুস্থে চা খেয়ে পান জরদা মুখে পুরলেন। জরদাটা ভাল নয়। কর্তা থাকলে পাঁচ দোকান খুঁজে এনে দেন; তিনি নেই, ছেলেকে বলেছিলেন উমাশশী, ছেলে যা পেয়েছে হাতের কাছে এনে দিয়েছে ; বিশ্রী জরদা। দায়সারা কাজ। এসব থেকেই বোঝা যায়, কর্তা না থাকলে উমাশশীকে কেউ তোয়াক্কাও করে না।
চোখে চশমা এঁটে বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লেন উমাশশী। চিঠিগুলো গুছিয়ে নিলেন।
প্রথম চিঠিটা বাড়ি ছেড়ে যাবার দিন দুই পরে এসেছে। আবার একবার খুঁটিয়ে পড়লেন। উমাশশী আর উমাশশীর বাবাকে কী বিচ্ছিরি করে গালাগাল দিয়েছে দেখেছ। যেন পুলিশের মেয়েকে বিয়ে করে উনি বাঘের খাঁচায় ঢুকে পড়েছিলেন বেরুবার আর পথ পাননি, মেয়ে বাপে মিলে ওকে শুধু ভয় দেখিয়েছে, আঁচড়েছে, কামড়েছে।…ঠিক আছে কর্তা—ছেলের কাছে তুমি খুব সাধু সাজছ, নিরীহ গোবেচারি সাজছ। এ-রকম বেইমানি ধর্মে সইবে না। মা-বাপ মরা ছেলে, দেখতে শুনতে ভাল, বিদ্যেবুদ্ধি রয়েছে দেখে বাবা তোমায় যেচে জামাই করেছিলেন—নয়ত পাঁচ সাতটা অ্যাডভোকেট, ব্যারিস্টার ছেলে হাতে ছিল বাবার। কাঞ্চন ফেলে কাচ নিয়েছিলেন বাবা। অমন মানুষের গায়ে তুমি কাদা ছিটোলে! নিজের দোষটা দেখ না কেন গুপ্তবাবু? বিয়ে করেছিলে যখন তখন থাকার মধ্যে চাকরিটাই না হয় ছিল, আর কোনো সাংসারিক জ্ঞান ছিল তোমার? একটা ঘরভাড়া পর্যন্ত জোটাতে পারো না, বউকে নিয়ে আহ্লাদ করার ইচ্ছে। বাবা রাজি হননি বলে কত তেরিয়া-মেরিয়া। শ্বশুরবাড়ির ছায়া মাড়াবে না বলেছিলে। আমার বাবা তোমায় ধরে আনিয়েছিলেন। তাতে কোনো দোষ হয়েছে?…পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটতে বোলো না, তোমারই তাতে মাথা কাটা যাবে। আমার তখন প্রথম, পাঁচ ছ’ মাসে নষ্ট হয়ে গেল, আমি বিছানায় শুয়ে কেঁদে মরি আর তুমি স্বার্থপর ইয়ার বন্ধু নিয়ে নৈনিতাল বেড়াতে যাবার ফন্দি করছ। বাবা তোমায় ধরে আনিয়েছিলেন। বড্ড অন্যায় করেছিলেন আমার পুলিশ-বাবা? কোন একটা দলের সঙ্গে ক্যাম্প করতে গিয়েছিলে—যেখানে তোমার ঘাড় মটকাবার জন্যে মেয়ে জুটেছিল এক, দুজনে শীতের মধ্যে হু হু হি-হি করতে করতে আগুন সেঁকতে। এই নিয়ে অশান্তি করতে চেয়েছিলে তুমি। বলেছিলে, বাড়ি ছেড়ে চলে যাবে। বাবা তোমায় শাসিয়ে দিয়েছিলেন আড়াল থেকে। কত না গুণ ছিল তোমার গুপ্তবাবু। ছেলেমেয়েদের কাছে তো তোমার মতন নির্লজ্জ হয়ে সব কথা বলতে পারি না, তুমি আজ তাই আমার মুখে চুনকালি মাখাচ্ছ। মাখাও।
খুঁজেপেতে দ্বিতীয় চিঠিটাও সাজিয়ে নিলেন উমাশশী। পড়লেন আবার খুঁটিয়ে। ঠিকানা নেই। কিন্তু চিঠি থেকে বোঝা যাচ্ছে, পুরনো ধর্মশালা ছেড়ে কর্তা নতুন জায়গায় গিয়ে উঠেছেন। অন্য কোথাও। লিখেছেন, এখানে ঝরনা আছে, বন আছে, গাছে গাছে অজস্র পাখি। পুরনো এক শিবমন্দির। শিবমন্দিরের সামান্য তফাতে এক আশ্রম মতন। চার পাঁচটি সাধু সন্ন্যাসী থাকেন। সকলেই অস্থায়ী। এক দু’মাস করে থাকেন, আবার চলে যান। সেখানে কোনো এক মহাসাধুর সাক্ষাৎ পেয়েছেন কর্তা। তিনি নাকি গুপ্তবাবুকে বলেছেন, “তুমি তো চাঁদি ছিলে বেটা, কিন্তু তোমায় এখন সিসে বলে মনে হচ্ছে—তোমার জেল্লা কেউ নষ্ট করে দিয়েছে।”
চিঠিতে কর্তা লিখেছেন : “তোমার মাতাঠাকুরানীর গণ আমি জানি না। রাক্ষসগণ ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। আমি নরগণ। নর-রাক্ষসের লড়াইয়ে নরের পক্ষে জেতা সম্ভব নয়। তোমার মার জয় হইয়াছে ; আমি পরাস্ত হইয়া দলিত মথিত অবস্থায় পড়িয়া আছি। আমার আর জেল্লা কি করিয়া থাকিবে? তোমার মা আমায় সিসা করিয়া ছাড়িয়াছেন। বড়ই দুঃখ হয়, বুক ফাটিয়া যায়। আমার কী ছিল আর কী হইলাম। সোনা তামা হইয়া গেল। নদীটি মজিয়া নালা হইয়া গেলে এই প্রকারই হয়। তোমার প্রতি আমার উপদেশ, পুলিশের মেয়ে তো বটেই, এমন কি যে-মেয়ের চলনে-বলনে, আচারে-আচরণে বিন্দুমাত্র মদ্দানি ভাব দেখিবে, বুঝিবে সে তোমায় গলা ও বাহুর জোরে দাবাইয়া রাখিবে—কদাচ তাহাকে বিবাহ করিবে না। করিলেই মরিবে। তোমার ব্যক্তিত্ব সেই চণ্ডীস্বরূপা কন্যা অতি সহজেই আমের মতন চুষিয়া খাইবে।
আমি রীতিমত সুস্থ। এই স্থানের লাল আটার রুটি ও অড়হর ডাল যে কী অপূর্ব স্বাদের তাহা তুমি বুঝিবে না। ভিণ্ডির ঘেঁটটিও চমৎকার। কিঞ্চিৎ ছাগ দুগ্ধ পান করিয়াছি। উহা বড়ই উৎকট। মহাত্মাজি যা পারেন—সাধারণে তাহা কেমন করিয়া পারিবে। যাহা হউক, আমার জন্য চিন্তা করিও না। আমি শান্তিতে আছি। আমার বন্ধনদশা কাটিয়াছে ইহাই জগদীশ্বরের কৃপা। এখানে শীত পড়িয়াছে। ওখানে কি শীত পড়িল। শীত সমাগমে তোমার মা-জননী বাতব্যাধিতে কাবু হন। মাঝে-মাঝে আমি ভাবি, মনুষ্যরূপে না জন্মিয়া যদি বাতব্যাধিরূপে এ-সংসারে আসিতে পারিতাম আমার কিছু লাভ হইত। আমার কপাল মন্দ।”
উমাশশী চিঠিটা যথারীতি ভাঁজ করে খামে রেখে দিলেন। রাগে করকর করছিল চোখ, মাথাটাও দপদপ করছে। কিন্তু কার ওপর রাগ দেখাবেন? থাকত মানুষটা চোখের সামনে তো ঝাঁপ দিয়ে বুকের ওপর পড়তেন। নাগালের বাইরে গিয়ে আজ বলছেন আমি নাকি রাক্ষস, আর উনি নর। আমার হাতে পড়ে রুপোর তাল সিসে হয়ে গেছে? আজ এসব কথা তো লিখবেই। নেমকহারাম, অকৃতজ্ঞ। উমাশশীর হাতে পড়েছিল বলে বর্তে গিয়েছ। কিছুই তো ছিল না তোমার। এই ঘরবাড়ি, দুটো পয়সা গচ্ছিত রাখা, বড় মেয়ের বিয়ে সবই আমার জন্যে হয়েছে, তোমার কেরামতিতে নয়। ব্যারিস্টার বর ছেড়ে তোমার মতন হেজিপেজিকে বিয়ে করেছিলাম—আর আজ তুমি বলছ আমি রাক্ষুসি।
কাঁদতে ইচ্ছে করছিল উমাশশীর। কিন্তু কী হবে কেঁদে? কার জন্যে কাঁদবেন? ওই চোর, বাটপাড়, ভাগলু মানুষটার জন্যে?
তৃতীয় চিঠিটা বার করে নিলেন উমাশশী। এটা আবার আদিখ্যেতা করে মেয়েকে লেখা। পড়া চিঠি। আবার পড়লেন।
খুবই অবাক কাণ্ড, মানষুটা কোথাও দুদিন স্থায়ী হচ্ছে না।
আজ এখানে, কাল ওখানে। কোন পথ থেকে কোথায় চলেছে? হিমালয়ের দিকে নাকি? আগের বার যেখানে ছিল তার সামনে ঝরনা, বন, পাখি, শিবমন্দির কত কী! এবারে মেয়ের কাছে বর্ণনা করে লিখেছে, এক শেঠের বাড়ির দোতলার ঘরে রয়েছে। সামনে নর্মদা নদী। শয়ে শয়ে লোক সকাল থেকে স্নান পুজো-আর্চা করছে, সাধু সন্ন্যাসীদের আসা-যাওয়া, নর্মদা নদী তরতর করে বয়ে চলেছে, ঘাটের পাড়ে গাছের ছায়ায় সারাদিন ধুনি জ্বলে সাধুদের।।
কর্তা মেয়েকে লিখেছেন, “তীর্থে তীর্থে কত কী ছড়াইয়া রহিয়াছে। সংসারে থাকিলে জীব অন্ধ হয়, কিছুই দেখিতে পায় না। আমি যাহা দেখিতেছি তাহাতেই চমৎকৃত হইতেছি। এখানে এক বাঙালি সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। আঠারো বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া হিমালয়ের দিকে চলিয়া গিয়াছিলেন। বারো বৎসর গুহায় সাধনা করিয়াছেন। এখন আবার এই অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়ান। বয়স পঞ্চাশ হইবে। কী তেজপূর্ণ চেহারা। মহা পণ্ডিত ব্যক্তি, মস্ত সাধক। কিন্তু বড় বিনয়ী, নম্র, প্রাণখোলা।
স্বামীজি আমায় একটি দুটি উপদেশ দিয়াছেন। তোমার মঙ্গলের জন্যে লিখিতেছি। স্বামীজি বলেন, মানুষের কয়েক প্রকার স্বভাব আছে, সে কখনও কখনও বৃষ জাতীয় আচরণ করে, কখনও বৃশ্চিক জাতীয়। আবার কাহারও আকার প্রকার, আচার বিচার কুম্ভ জাতীয়। বৃষ জাতীয় মানুষ সংসারে খায় দায় ঘুমায়, কখনও কখনও সামনে পড়িলে গুঁতা মারে। বৃশ্চিক জাতীয় মানুষ ভীষণ, তাহারা শুধু কামড় দেয় না, বিষের জ্বালায় জ্বালায়। আর কুম্ভ জাতীয়রা গোবেচারি। তাহারা সহজেই ফাটিয়া যায়।
তুমি আমার কনিষ্ঠা কন্যা। তোমার স্বভাব যদি তোমার গর্ভধারিণীর মতন হয় তবেই মরিবে। তোমার মা যে বৃশ্চিক জাতীয় মানুষ তাহাতে আমার কোনো সন্দেহ নাই। তাঁহার কামড় যত, বিষও তত। আমি তো তাঁহাকে সজারুও বলিতে পারি। কাছে গেলে তাঁহার গা ফোলে, কাঁটা দিয়া বিদ্ধ করেন। তুমি কখনও মার স্বভাব গ্রহণ করিও না। আমাদের দেশের মেয়েদের নম্র, বিনীত, মিষ্টভাষী হইতে হয়। ইহাতেই তাহারা সকলকে সুখী করে নিজেও সুখী হয়। তুমি অন্য সংসারে গিয়া অন্যদের সুখী করো, নিজে সুখী হও—ঈশ্বরের কাছে ইহাই আমার প্রার্থনা। তুমি যে কেমন তাহা আমি জানি, তবু ভয় হয় তোমার মাতাঠাকুরাণী না তোমায় দলে টানিয়া লন। বৃশ্চিকম্ বিভেতি। সংস্কৃত ব্যাকরণ বিদ্যা আমার নাই। শুদ্ধ করিয়া নিবে। মোদ্দা কথাটি এই, বৃশ্চিক হইতে সাবধান।
আমার অল্পস্বল্প কাশি হইয়াছিল। এই অঞ্চলে শীত আসিয়াছে। ঠাণ্ডা লাগিয়াছিল বোধ হয়। মিছরির কৎ করিয়া আদা গোলমরিচ সহযোগে খাইয়াছি। কাশি আরাম হইয়াছে। মনে আমার স্ফূর্তি, প্রাণে মুক্তি। বেশ আছি। মোটা মোটা চাপাটি, বেগুনপোড়া, ছোলার ডাল, দহি দিন দুই খাইলাম। ভালই লাগিল। আধ লোটা দুধও জুটিয়াছিল গতকাল। ঘুমটুম ভালই হইতেছে।
তোমার মাকে বলিবে তিনি যেন আমার বিছানাটি গুটাইয়া ছাদে তুলিয়া দেন। আমার খাটটি ঘর হইতে বাহির করিয়া কলাবাগানে ফেলিয়া আগুনে দিবার ব্যবস্থা করেন। আমার যাহা কিছু আছে দানধ্যান করেন। সংসারের বাইরে যে শান্তি পাইয়াছি তাহা ছাড়িয়া কোন মূখে আর গৃহে ফেরে।”
উমাশশী চিঠি শেষ করে চোখ বুজে শুয়ে থাকলেন। মাথার মধ্যে টনটন করছে, ঘাড়ের কাছটায় ব্যথা। সর্বাঙ্গ জ্বালা করছে রাগে। এ কেমন শত্রুতা? দূর থেকে আড়াল থেকে আমার শত্রুতা করছ? সাধ্য থাকে, সাহস থাকে সামনে এসে দাঁড়াও। কে বৃশ্চিক আর কে কুম্ভ তোমায় দেখাচ্ছি। এমন অসভ্যতা মানুষে করে। ইতরোমির শেষ নেই। নিজের ছেলেমেয়েদের তুমি তাদের মা’র পেছনে লাগাচ্ছ? ছি ছি, ঘেন্নায় মরি।
অভিমানে উমাশশীর চোখে জল এল। দু’ফোঁটা কেঁদে চোখ মুছে নিলেন।
স্বামীর জন্যে চোখের জল উমাশশী অনেক ফেলেছেন। তখন বয়েস ছিল ফেলার, জলও ছিল পর্যাপ্ত। এ-বয়েসে আর কতই বা কান্নাকাটি করতে পারেন, সেই যে কর্তা ঢং করে গাইতেন ‘নয়নের বারি রেখেছ নয়নে’—সেই বারিও এখন শরীরের আর পাঁচটা পদার্থর মতন কমে এসেছে। কমে এসেছে, না অন্তঃস্রোতা হয়েছে তা অবশ্য উমাশশী বুঝতে পারেন না। তখন হাউমাউ করে কাঁদলেও বলার কেউ ছিল না ; ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট—তারা অতশত বুঝতে পারত না, উমাশশী অন্য কোনো কথা বলে কিংবা ছুতো দেখিয়ে প্রাণভরে কেঁদে নিতে পারতেন। এখন কি আর পারেন! ছেলেমেয়েরা বুঝতে পারবে, মা, বাবার জন্যে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। দেখে আড়ালে হাসাহাসি করবে।
কান্নাটা তাই উমাশশীর বুকে বুকে রইল। নিজের ঘরে বসে বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলেন, টপ টপ করে জল পড়ে চোখ বেয়ে, আঁচলে মুছে নেন। বুকের তলায় কষ্ট হয়, দুপুরে শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবেন—কোথা দিয়ে কেমন করে কর্তাকে ধরবেন, বুঝতেও পারেন না। বেনারস, এলাহাবাদ, হিল্লি-দিল্লি কোথায় গিয়ে রয়েছেন জানতে পারলেও একটা কথা ছিল—উমাশশী না হয় ছুটতেন, কিন্তু গুপ্তবাবু যে কোথায় তা জানার কোনো পথ রাখেননি।
উমাশশী একেবারে হাল ছেড়ে দেবার মানুষ নন। যদি তাই হতেন তবে কোন কালেই গুপ্তবাবুকে ছেড়ে দিতেন, আর গুপ্তবাবুও খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে মুক্ত বিহঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়াতেন। উমাশশী অত বোকা বা কাঁচা নন, নিজের পায়ে কুড়ুল মেরে গুপ্তবাবুকে স্বাধীন মুক্তপুরুষ হতে দেননি। পুরুষ মানুষ কেমন জিনিস তা তিনি জানেন, হাতের ফাঁক দিয়ে একবার গলে পড়ল তো পড়লই, কোন জলে গিয়ে ডুববে, তা কেউ জানে না। কার সাধ্য আর তাকে খুঁজে বার করে!
উমাশশী স্বামীকে আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলতে দেননি, খুব সাবধানে মুঠোর মধ্যে ধরে রেখেছিলেন। মুঠো একটু আধটু আলগা হলেই বুঝেছেন গুপ্তবাবু গলবার চেষ্টা করছেন। সঙ্গে সঙ্গে মুঠো আরও শক্ত হয়েছে। গুপ্তবাবু বুঝে নিয়েছেন, তিনি যদি যান ডালে ডালে উমাশশী ঘোরেন পাতায় পাতায়।
মানুষটাকে বরাবর এইভাবে বেঁধে রেখেছিলেন উমাশশী। বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন—তোয়াক্কাও করেননি ; পালাবার পথ ছিল না কর্তার, খোঁয়াড়ের জীব ঠিকই ধরা পড়ে যাবে, উমাশশী জানতেন। আজ বাবা নেই, উমাশশী অসহায়, আর ঠিক এই সময়ে যখন উমাশশীর মনে কিছুমাত্র খল ছিল না, দুশ্চিন্তা ছিল না, তখন কর্তা তাঁকে ফাঁকি দিয়ে পালালেন। উমাশশী ভাবতেই পারেন না। এই বয়সে কেউ পালায়! যখন বয়েস ছিল পালাবার তখন যদি পালাতে পারতে, তোমায় আমি ত্যাজ্য করতুম। তখন তো মুরোদ ছিল না। এখন আমায় অক্ষম দেখে খুব সাহস দেখালে!
কুড়ি বাইশটা দিন তো কাটল। উমাশশী তো পাথর নন, মানুষ। তাঁরও গায়ে রক্তমাংস আছে। তুমি যতই তাকে রাক্ষসগণ বল, বল না কেন বৃশ্চিকের জাত, তার স্বভাব চরিত্র নিয়ে খোঁচা মার, তবু সে কেমন করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারে! হাজার হোক, মানুষটি জোয়ানমদ্দ নয়, বয়েস হয়েছে, বুড়ো—; তার এখন নিয়মে থাকার কথা, একটা সহ্য হয় অন্যটা হয় না, আরাম-আয়াস ধরাবাঁধা দরকার ; সেই মানুষ লাল আটার রুটি, অড়হর ডাল, ঢেঁড়সের তরকারি আর ছাগলের দুধ খাচ্ছে, মাটিতে কম্বল পেতে শুয়ে আছে, ভাবলেই উমাশশীর বুকের মধ্যে কেমন যেন করে। তার ওপর লিখেছে, সর্দিকাশি হয়েছিল—মিছরির কৎ আর আদা খেয়ে আরাম হয়েছে।
উমাশশী বুঝতে পারছেন, একটা সর্বনাশ না করে গুপ্তবাবু ছাড়বেন না। অত জেদ, অত তেজ, স্ত্রীর ওপর পুষে রাখা তিরিশ বছরের গায়ের জ্বালা মেটাতে গিয়ে কর্তা কোথায় কোন ধর্মশালায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়বেন—তখন উমাশশীর ডাক পড়বে। ভবিষ্যতটা উঁকি মারলেই বুক কেঁপে ওঠে উমাশশীর। অর্শের রোগী, ওদিকে আবার শ্লেষ্মার ধাত, সামান্য গোলমাল হলেই বুকে কফ জমে, অল্পস্বল্প ডায়েবেটিস—, ঠাকুরের কত অঙ্গে কত খুঁত,—সেই মানুষ গিয়েছেন সংসার ত্যাগ করতে। আসলে সবই উমাশশীকে ভোগাবার জন্যে। কিন্তু এ-কথা কে কর্তাকে বোঝাবে—অত তেজ ভাল নয়, এটা আহম্মুকি। নিজে যখন চোখ উলটে পড়বে—তখন তোমার ভোগান্তিও কম হবে না।
কুড়ি বাইশ দিনের মাথায় আবার চিঠি এল। ছেলেমেয়েরা চিঠি লুকোয় না। মেয়েই চিঠিটা এনে দিল। উমাশশী তখন রান্নাঘর ঘুরে সবে নিজের ঘরে এসেছেন, একটু জিরিয়ে নেবেন, আশা এসে চিঠিটা দিল।
উমাশশী বললেন, “পিয়ন এসেছিল?”
আশা মা’র মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন যেন ইতস্তত করল। বলল, “না। দাদা একটু বেরিয়েছিল, পোস্ট অফিস থেকেই চিঠি নিয়েছে।”
“কোথায় দাদা?”
“ঘরে।”
উমাশশী খামটা উলটে পালটে দেখছিলেন। যথারীতি খামের মুখ ছেঁড়া। চশমা দিতে বললেন মেয়েকে।
আশা চশমা এনে দিল।
চশমা চোখে দিয়ে উমাশশী খামের ঠিকানাটা যেন একটু বেশি নজর করেই দেখলেন ; তারপর ডাকঘরের ছাপ। ব্যাপারটা তাঁর কাছে খুবই আশ্চর্যের মনে হয়। একটা দুটো নয়, আজ কুড়ি বাইশ দিনে চার পাঁচটা চিঠি এসেছে কর্তার, সব কটাই খামে, কিন্তু সবকটা চিঠিরই ডাক টিকিটের ওপর মারা ডাকঘরের ছাপ এত অস্পষ্ট কেন? কেন একটারও ছাপ পড়া যায় না? ছাপটা পড়া গেলে বোঝা যেত কর্তা কোথায় আছেন।
উমাশশী হঠাৎ ছেলেকে তলব করলেন। আশা দাদাকে ডাকতে গেল। উমাশশী চিঠিটা বার করলেন। সেই একই ব্যাপার, নিজের কোনো পাত্তা দেননি কর্তা, নি-ঠিকানা চিঠি লিখেছেন ছেলেকে। তপু এল। আশাও পিছু পিছু এসেছে। উমাশশী ছেলের দিকে তাকালেন। চোখে বিরক্তি। “তুমি পোস্ট অফিসে গিয়ে চিঠি নিয়েছ?”
তপু মাথা দোলাল। “চুল কাটতে গিয়েছিলাম সেলুনে। পোস্ট অফিস থেকে নিয়ে নিলুম চিঠিটা।”
“পোস্টমাস্টারকে জিজ্ঞেস করলে না কেন?”
তপু মা’র চোখে চোখে তাকাল না। বলল, “কী?”
“এই যে তোমার বাবার চিঠিগুলো আসছে—এগুলো আসছে কোথা থেকে?”
তপু যেন থতমত খেয়ে গেল। বলল, “কেন? বাবা যেখান থেকে লিখেছে।”
“সেই জায়গাটা কোথায়?” উমাশশী ছেলেকে ধমকে উঠলেন। “একটা চিঠিরও টিকিটের ওপর ছাপ পড়া যায় না কেন?”
তপু রীতিমত ঘাবড়ে গেল। আশার দিকে তাকাল একবার। তারপর ঢোঁক গিলে বলল, “কি জানি। পোস্টমাস্টারবাবুকে জিজ্ঞেস করলে তিনি কেমন করে বলবেন। ছাপ তো পড়াই যায় না। আমার মনে হয় বাবা আর. এম, এস-এ চিঠি ফেলে।”
উমাশশী বললেন, “কেমন করে বুঝলে?
তপু বলল, “আমি দু’একটা খামে ‘আর আর’ দেখেছি। না রে আশা?”
আশা ঘাড় হেলিয়ে বলল, “আগের চিঠিটাতেই ছিল।”
উমাশশীর পছন্দ হল না। বললেন, “কাল পোস্ট অফিসে গিয়ে মাস্টারমশাইকে জিজ্ঞেস করবে। তিনি তো তোমাদের বাবার ইয়ার-বন্ধু ছিলেন। জিজ্ঞেস করবে, এ-রকম বে-আইনি চিঠি কেন আসে?”
আশা বলল, “বে-আইনি বলা যাবে না, মা।”
“কেন?”
“ছাপ তো থাকে।”
“তুমি আমায় আইন শেখাবে! আমার বাবার কাছে আমি অনেক আইন গুলে খেয়েছি।”
আশা চুপ করে গেল।
তপু কি যেন ভেবে নিয়ে বলল, “পোস্টমাস্টারবাবুকে বলব মা, যে বাবা রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন?”
উমাশশী আরও বিরক্ত হলে, অসহ্য লাগল তাঁর। বললেন, “তা আর বলবে না? বদ্যির ঘরে কি দামড়াই জন্মেছে! ঘরের কথা পাড়ার লোককে না বলে বেড়ালে তোমার বাবার মান আর বাঁচছে না।”
তপু অধোবদন হল।
উমাশশী বললেন, “তোমাদের বাবার এমনিতে তো আর গুণের ঘাটতি ছিল না, এখন এই বুড়ো বয়েসে ভীমরতি ধরেছে, চুরি চামারি করে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছে—এটা আবার শহরময় ঢ্যাঁঢড়া পিটিয়ে বলে বেড়াও—তাতে তোমাদের বাবার আরও চারটে পা গজাবে। মুখ্যু, দামড়া কোথাকার।”
আশা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছিল।
তপুও পালাবার চেষ্টা করছিল, উমাশশী বললেন, “আমি পই পই করে না বলেছি, তোমাদের বাবা নিমাইসন্ন্যাস হয়েছে একথা কাউকে বলার দরকার নেই। শুনলে লোকে হাসাহাসি করবে, ছি ছি করবে। তোমাদের বাবা ক’দিনের জন্যে বাইরে গেছেন দরকারে—এর বেশি কিছু বলার দরকার তো করে না।”
তপু ঢোঁক গিলে বলল, “তাই তো বলি—কেউ জিজ্ঞেস করলে।”
“তাই বলো। যাও।”
তপু মা’র চোখের সামনে থেকে সরে পড়তে পারলেই যেন বাঁচে। সরে সরে ঘর ছেড়ে পালাল।
ছেলেমেয়েরা চলে যাবার পর উমাশশী কয়েক মুহূর্ত দরজার দিকে তাকিয়ে বসে থাকলেন। রাগ, ক্ষোভ, অশান্তিতে তাঁর মুখচোখ অপ্রসন্ন দেখাচ্ছিল। এই রকম ছেলেমেয়ে তিনি আর দেখেননি।
একটা বুড়ো মানুষ, ঘরের কর্তা, তোদের বাবা—বাড়ি ছেড়ে চলে গেল, দেখতে দেখতে প্রায় মাস পুরতে চলল, অথচ তোদের কোনো গা নেই। একটা দিনের জন্যেও দেখলাম না, তোরা তোদের বাপের জন্যে ছটফট করিস, মুখ শুকনো করে বসে থাকিস! চারবেলা খাচ্ছিস দাচ্ছিস, সাজন-গোজন করছিস, রেডিয়ো বাজিয়ে গান শুনছিস আর বাইরে বাইরে আড্ডা ইয়ার্কি মেরে বেড়াচ্ছিস! তোদের দেখলে মনে হয়, গলা কেটে কেটে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে আসি। বাপ বাড়ি নেই, সে-মানুষটা কোথায় কোন চুলোয় ছাতু ছোলা খেয়ে মাটিতে শুয়ে মরছে, আর তোরা দুজনে কেমন যে যার ঘরে চাদর মুড়ি দিয়ে নাক ডাকাচ্ছিস!
একেই বলে ছেলে মেয়ে! স্বার্থপরের দল! মা-বাপকে শুধু শুষতেই পারিস তোরা, তোদের মায়া মমতা ভালবাসা ভক্তি কিছু নেই। আজকালকার ছেলেমেয়েদের এই রীতি নীতি। উমাশশীদের সময় অন্যরকম ছিল। উমাশশী নিজেই বাবা বলতে অজ্ঞান ছিলেন। অবশ্য বাবাও ছিল সেইরকম। তোদের বাবার মতন চোর জোচ্চোর বাটপাড় বাবা নয়।
আসলে যেমন বাপ তার তেমনই ছেলেমেয়ে, উমাশশীর দুর্ভাগ্য, তিনি আর মাথা খুঁড়ে কেঁদেকেটে কী করবেন! ভগবান যার কপালে যা লিখেছেন তাই তো হবে।
বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে ভারী বুকে উমাশশী এবার চিঠিটার ওর চোখ রাখলেন। ছেলেকেই লেখা হয়েছে।
কর্তা আর নর্মদার তীরে নেই। আগের আশ্রমটিও ত্যাগ করেছেন। লিখেছেন, এখন তিনি পরিব্রাজক। কোথাও আর স্থিত হচ্ছেন না। শুধু এগিয়ে চলেছেন।
“আমায় যে কোন বৈরাগ্য দেবতা অলক্ষ্য হইতে হাতছানি দিতেছেন তাহা আমি জানি না, তপু। আমি শুধু আমার ঝোলাঝুলিটা কাঁধে লইয়া তাঁহার ডাকে চলিতেছি। আমায় দেখিলে তোমাদের অবাক হইবার কথা। গালে দাড়ি, হাতে লাঠি, পায়ে কেড্স জুতা, কাঁধে একটা বোঁচকা। আমার কোথাও বিরাম নেই, চলিতেছি আর চলিতেছি। কখনও রেলে, কখনও বাস গাড়িতে, কখনও পদব্রজে। আমার সহিত একদল তীর্থযাত্রীর পরিচয় ঘটিয়াছিল। এই দলটি কম নয়, জনা পনেরো হইবে। নারী পুরুষ উভয়েই আছে। তবে নারীর সংখ্যা কম দুই তিনজন মাত্র। পথে ইহাদের সঙ্গে দেখা ও পরিচয়। শুনিলাম তাঁহারা উত্তর হইতে নামিয়া আসিতেছেন, এখন দক্ষিণে যাইবেন। তাঁহাদের নিকট জানিলাম, সাধুসঙ্গের প্রকৃষ্ট স্থান হিমালয়, পথে পথে কত সাধুসজ্জন। তাঁহাদের নিকট বরফানিবাবা নামের এক মহাপুরুষের নাম শুনিলাম। ইনি বরফের মধ্যে সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া থাকেন বলিয়া লোকে ইহাকে বরফানিবাবা বলে। তাঁহার যে কত বয়েস তাহাও জানা যায় না। একশো সোয়াশে বছরও হইতে পারে। যাহা হউক, আমি এখন উত্তরের পথে পাড়ি জমাইয়াছি, হরিদ্বার হইয়া হিমালয়ের দিকে যাত্রা করিব। হিমালয় আমায় টানিতেছে।
একটি অদ্ভুত ঘটনার কথা তোমায় জানাই। রেলগাড়িতে এক ভদ্রলোকের সহিত ঘটনাচক্রে আমার আলাপ হইয়া যায়। তাঁহার পরিচয়, তিনি একসময় সিমলায় গভর্নমেন্টের হোমরা চোমরা অফিসার ছিলেন।
ভদ্রলোক জীবনে অনেক দুঃখশোক পাইয়া এখন সংসারধর্ম ত্যাগ করিয়াছেন, উচ্চশ্রেণীর তন্ত্রসাধনা করেন। তাঁহার কিছু ক্ষমতা জন্মিয়াছে। খগেনবাবু আমায় বলিলেন, আমার আত্মার ওপর একটা মোটা আবরণ ছিল, যেমন কাঠবাদামের ওপর শক্ত পুরু খোসা থাকে। এই খোসাটি আমার চৈতন্যকে এমনভাবে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল যে আমার নাকি চৌরাশি জন্মের লক্ষণ ছিল। জীব হইয়া আমাকে নাকি চৌরাশি বার ভ্রমণ করিতে হইত। পরমেশ্বরের কৃপায় আমার সে দুভার্গ্য ঘুচিয়া গিয়াছে, আমি মুক্তি পাইয়াছি। এখন আমার চৈতন্য কাহারও কবজায় নাই, আমার কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত। খগেনবাবু বলিয়াছেন, অচিরেই আমি কোনো উন্নত সাধকের সাক্ষাৎ পাইব। কর্মবিপাকে আমি পাতক ছিলাম, এবার সাধক হইব।
খ-বাবু আমায় আরও একটি অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখাইলেন। তিনি একটি আরশি বাহির করিয়া দিলেন, ছোট আরশি, আঙুল চারেক তাহার মাপ। আরশির ওপর কালচে রঙের কিছু মাখানো। আমার কপালে তাঁহার বুড়া আঙুল কয়েক মুহূর্ত ছোঁয়াইয়া রাখিলেন, তাহার পর আঙুল সরাইয়া আরশিটি দেখিতে বলিলেন। প্রথমটায় কিছু দেখিতে পাইলাম না। পরে দেখিলাম, কী আশ্চর্য, আরশির মধ্যে তোমাদের মাতাঠাকুরাণী। সাইজটা ছোট। দেখিলাম, তোমাদের গর্ভধারিণী বিছানার ওপর শুইয়া আছেন, বালিশের পাশে পানের ডিবা, জরদার কৌটা। তিনি হঠাৎ উঠিলেন, এবং কোথা হইতে একটা খাঁড়া যোগাড় করিয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিলেন। ভয়ে আমি আরশি ফেলিয়া দিলাম। খ-বাবু বলিলেন, গৃহী হইবার বিন্দুমাত্র বাসনাও যদি অন্তরে থাকে, ত্যাগ করুন। গৃহে ফিরিলে আপনি অবশ্যই অনুশোচনা করিবেন।
বাবা তপু আমি মন্ত্র তন্ত্র বিশ্বাস করিতাম না। কিন্তু খ-বাবুর আরশিতে তোমার মা-জননীর যে মূর্তি দেখিলাম, তাহাতে আমার হৃদকম্প হইল। এ-মূর্তি ভুলিবার নয়। পূর্বেও কত দেখিয়াছি, তবে যথার্থ খড়গধারিণী রূপে দেখি নাই, এই প্রথম, দেখিলাম। দেখিয়া বন্ধুবাবুর সেই গীতটি মনে পড়িল :‘নাচিছে তুরঙ্গ মোর রণ করে কামনা…’
তোমার মাতাঠাকুরাণীকে বলিবে, তাঁহার তুরঙ্গ যতই নাচুক না কেন তিনি আর ইহজীবনে রণসাধ মিটাইতে পারিবেন না। আমি তাঁহার খড়গ ও আস্ফালন হইতে বহুদূরে। তিনি আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিবেন না। বরং ধর্মমতে ও শাস্ত্রমতে আমি যখন জীবিত—তখন বৃথা তুরঙ্গ না নাচাইয়া মহাশয়া যেন শয়নে-ভোজনে-তাম্বুলে চর্বণে তৃপ্ত থাকেন। তাঁহার ক্রোধ ও ক্লেশের কোনো কারণ নাই। আপদ বিদায় লইয়াছে, ইহাতে তো তাঁহার শান্তি পাইবার কথা।
আমি পরে তোমায় পত্র লিখিব। এইস্থানে ইতি করিতেছি। তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিও।”
উমাশশী চিঠিটা বার দুই পড়লেন। পায়ের নখ থেকে ব্রহ্মতালু পর্যন্ত গনগনে আঁচের মতন জ্বলছে। ঘাড় টনটন করছিল। কপাল ফেটে যাচ্ছে।
চোখের পাতা বন্ধ করে যেন নিজেকে খানিকটা সামলবার চেষ্টা করলেন।
সামলানো কি যায়! এই অসভ্যতা, ছোটলোকমির কোন জবাব উমাশশী দেবেন? পরিব্রাজকের এই কি লক্ষণ? যে-লোকের নাকি চৌরাশি জন্মের আর ভয় নেই, যার চৈতন্য জেগেছে—সেই লোক এমন সব নোংরা অসভ্য বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি কথা লেখে? তাও আবার ছেলেকে!
উমাশশী আরও খানিকটা বসে থেকে উঠলেন। চোখে মুখে মাথায় জল ছিটিয়ে আসলেন। পা টলছিল উমাশশীর। গা দুলছিল। কলঘরে গিয়ে চোখে মুখে ঘাড়ে ভাল করে জল দিলেন। আঁজলা করে জল নিয়ে মাথায় থাবড়ালেন। জ্বালা কি যায়? না এই আগুন ভাবটা?
কলঘর থেকে বেরিয়ে কামিনীকে ডাকলেন। জল, পান দিতে বললেন।
ছেলেমেয়েদের গলা পাওয়া যাচ্ছে। হা হা হি হি করছে দুজনেই। রেডিয়ো বাজছে। কোনো শোক তাপ দুশ্চিন্তা উদ্বেগ নেই। ওদের বাপ এই দুই ছেলে মেয়েকে আস্কারা আর আদর দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলেছিল। যেন ইয়ার বন্ধু। যারা তার বাপকে চিরটা কাল ইয়ার-বন্ধুর মতন পেয়েছে—তারা আর কতটুকু বুঝবে বাবা কী জিনিস।
এখনও ছেলেমেয়েদের কোনো জ্ঞান হল না, হুঁশ হল না, হবে, ঠিকই হবে—যখন আর এ-জগতে বাপ-মা বলে মানুষ দুটো থাকবে না—তখন হবে। যত সব অকর্মা, হারামজাদার দল।
নিজের ঘরে ফিরে আসতে আসতে উমাশশীর মনে হল, তিনি একটা মস্ত ভুল করেছেন। এই তো মাস দুই তিন আগে আশার একটা সম্বন্ধ এসেছিল বিয়ের। সতু ঠাকুরপো কলকাতা থেকে চিঠি লিখেছিলেন। ছেলের অন্য গুণ সবই ছিল, দোষের মধ্যে সে চেহারায় বেঁটে, রংটা কালো, একটু বাউণ্ডুলে গোছের, উমাশশী এক কথায় না বলে দিলেন। বেঁটে, কালোকেষ্ট জামাই তিনি করবেন না। সারদা গুপ্ত নিমরাজি ছিলেন। উমাশশীর চোখে তখন নিজের কর্তার চেহারাটা লেগে আছে। ফরসা রং, লম্বা চওড়া চেহারা। যৌবনকালে ওই চেহারা যে কী ছিল, তা উমাশশীই জানেন। স্বামীর গা ধুয়ে জল খেলেও যেন তৃপ্তি লাগত। নিজের স্বামীর মতন যে জামাইও জুটবে, উমাশশী তেমন আশা করতেন না। তবু নিজে যেমন পেয়েছিলেন মেয়েকে তার অর্ধেক যদি না দেন তবে মেয়ে কি মনে করবে! বড় মেয়েকে তো ভালই দিয়েছেন। ছোট মেয়ের বেলায় অন্য নজর হলে চলবে কেন?
উমাশশীর এখন মনে হচ্ছিল, তিনি ভুল করেছেন। আশার বিয়ে দিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল। যার বাবা এমন দায়িত্বহীন, নির্বোধ ; যে-মানুষ ছেলেমেয়েকে সৎ শিক্ষার বদলে অসৎ শিক্ষাই দেয়—তার বাড়িতে আইবুড়ো মেয়ে রাখা উচিত নয়। ওই মেয়ে রাখা উচিত নয়। ওই মেয়ে এখন গলার কাঁটা হয়ে আটকে থাকবে। বিয়েটা দিয়ে দিতে পারলে উমাশশী ঝাড়া হাত-পা হতে পারতেন। কিন্তু তিনি কেমন করে বুঝবেন, মেয়ের বাপ, বুড়ো-মদ্দ, তার ভেতরে ভেতরে এত ফন্দি ছিল। ঘর ছেড়ে সে পালাবে।
কামিনী জল এনে দিল। পান!
উমাশশী জল খেলেন। পান জরদা মুখে দিলেন।
শীত পড়ছে ধীরে ধীরে। খোলা জানলা দিয়ে টকটকে রোদ দেখা যায়। কাক চড়ুই ডাকছে। লাল করবী ফুলের গাছটা মাথা তুলে দিব্যি রোদ পোয়াচ্ছে। পাশেই এক কাঠচাঁপা। কর্তা শীতের দিন কাঠচাঁপা গাছের তলায় চেয়ার পেতে বসে বই পড়তেন। গাছতলাটা ফাঁকা। বিছানায় বসলেন উমাশশী। চিঠিটা বালিশের তলায় চাপা দেওয়া।
দুপুরে চিঠিটা আরও একবার পড়বেন উমাশশী। এখন আর পড়ে কাজ নেই।
পুরুষ মানুষ এই রকমই হয়। এমন কিছু বয়েসে পাকা গিন্নি হয়ে স্বামীর সংসারে তিনি আসেননি। তবু যখন থেকে এসেছেন তখন থেকেই হাল ধরেছেন সংসারের; বলতে নেই—নিজের আঁচলের আড়ালে রেখে যেন কর্তাকে এতটা পথ বয়ে এনেছেন। কোনো কিছু বুঝতে দেননি। সেই কর্তা আজ তাঁকে বলেছেন, কাঠবাদামের শক্ত খোসা, বলেছেন তিনি নাকি পাতক হয়ে ছিলেন এতকাল! একেই বলে নেমকহারাম। তোমায় কোন খ-বাবু আরশি দেখাল, আর তুমি দেখলে—তোমার সাতপাকের বউ বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে শুয়ে পান চিবোচ্ছে! বলিহারি তোমার খ-বাবুকে! যেমন নাপিত সে, তেমনি তার আরশি। এসো একবার, নিজের চোখে দেখে যাও না গুপ্তবাবু, তোমার যে পরম শত্রু, যার পাল্লায় পড়ে তোমার সব গিয়েছে—সেই উমাদাসী কোন আরামে শুয়ে বসে দিন কাটাচ্ছে! খাঁড়া নিয়ে তোমায় তাড়া করতে কোনোদিনই যাইনি বাপু, তেমন শিক্ষা আমার মা-বাবা দেয়নি। তুমিই বরং আমার গা গতরের ছাল ছিঁড়ে ছিঁড়ে ডুগডুগি বানিয়ে বাজিয়েছ এতকাল!
উমাশশীর বুকে এতই কষ্ট হচ্ছিল যে তিনি গায়ের আঁচল নামিয়ে দিলেন, জামার বোতাম খুলে আলগা করে দিলেন সব, তারপর বুকের ওপর ডান হাতটা জোরে জোরে বোলাতে লাগলেন।
মনে পড়ল, গুপ্তবাবু বাড়ি ছেড়ে পালাবার আগের দিন সাত সকালে এই বুড়ি মাগির কাছে এসে নেচে নেচে খাটো গলায় কত গান ধরেছিলেন। আবার বলেন কিনা গীতগোবিন্দের গান, উমাশশী সারা জীবন ধরে কর্তার অনেক গোবিন্দগীত শুনেছেন, বেহায়াপনা তাঁর জানা আছে। কম বয়সে সবই মানায়, ভালও লাগে, কিন্তু এই বুড়ো বয়সে কোন বেহায়া বুড়ি বউয়ের কাপড়ছাড়া দেখতে দেখতে গান গাইতে পারে—‘ঘটয়তি সুঘনে কুচ-যুগ-গগনে…!’
উমাশশী বুকের ব্যথা সামলাতে সামলাতে আড় চোখে নিজের বুক দেখলেন। কর্তা নেই, সারা বুক টনটন করে উঠল। কে জানত, গুপ্তবাবু এমন করে বুকে শেল মারবেন। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উমাশশী যেন গুপ্তবাবুকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, এক মাঘে শীত পালায় না কর্তা, তোমার জন্যেও শীত পড়ে থাকল।
উমাশশী এবার বড় মেয়েকে নিজেই একটা চিঠি লিখলেন। তাঁর সাংসারিক জ্ঞান প্রখর। মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে কখনও বাপের বাড়ির কেচ্ছা কেলেঙ্কারি জানাতে নেই। মেয়ের গলা কাটা যাবে লজ্জায়, হেনস্থার শেষ থাকবে না। যে যাই বলুক, মেয়েদের বাপের বাড়ি আর শ্বশুরবাড়ি হল তেল আর জলের মতন, কোনোদিন এই দুইয়ে মিশ খায় না।
বড় মেয়েকে চিঠি লেখার আগে উমাশশী অনেক ভেবেছিলেন। বড় মেয়ে খানিকটা মায়ের ধাতের; যদিও বাপ বলতে বরাবর অজ্ঞান ছিল—তবু অন্য দুজনের চেয়ে মায়ের দুঃখকষ্ট সে বুঝত খানিকটা। বিয়ের পর মেয়েরা আরও যেন মা-দরদি হয়। উমাশশী বড় মেয়েকে বিয়ের পর দেখেশুনে সেটা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন।
বড় মেয়েকে আগেও চিঠি লেখা হয়েছে। লিখেছে তার ভাইবোনেরা। উমাশশী নিজে সে-চিঠি দেখেছেন। তাঁরই কথা মতন লেখা। গুপ্তবাবুর গৃহত্যাগের কোনো সংবাদ হয়নি, শুধু লেখা হয়েছিল, তিনি ক’দিনের জন্যে বাইরে গিয়েছেন। কোথায় গিয়েছেন তার কোনো হদিশ দেওয়া হয়নি। মেয়ের জবাবও দেখেছেন উমাশশী। আর পাঁচটা খবরের সঙ্গে জানতে চেয়েছে, তার বাবা ফিরে এসেছে কিনা! এরপর আর কোনো চিঠি এ বাড়ি থেকে যায়নি।
উমাশশী ভেবেচিন্তে দেখলেন, বড় মেয়েকে আর একটা চিঠি লেখা দরকার। সরাসরি না হলেও মেয়েকে জানানো দরকার যে তাদের বাবার মাথায় হিমালয় টিমালয় বেড়াতে যাবার শখ চেপেছিল। কর্তা এখন বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন। খবরটা জানিয়ে না রাখলে পরে কোন ফাঁক দিয়ে কী বেরিয়ে পড়বে বলা যায় না।
তা ছাড়া উমাশশীর আরও একটা ভয় হচ্ছিল। গুপ্তবাবুর জ্ঞানগম্যি নেই। এই বাড়িতে যেমন ছেলেমেয়েদের চিঠি লিখছেন, তেমনি হুট করে বড় মেয়েকেও তো চিঠি লিখতে পারেন। সেখানেও হয়ত জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি গৃহত্যাগ করেছেন। কিছু বলা যায় না। যদি তাই দিয়ে থাকেন তবে বড় মেয়ে এতদিনে সবই জানতে পেরেছে। জামাইও জেনেছে। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই, গুপ্তবাবু গৃহত্যাগের কারণ হিসেবে যে-লোকটিকে যোলো আনা দায়ী করেছেন সে-মানুষ তো উমাশশী।
যাই হোক বড় মেয়ের কাছ থেকে আর কোনো চিঠি আসেনি। উমাশশীও বুঝতে পারছেন না, মেয়ে তার বাপের কীর্তির কতটুকু জেনেছে বা জানেনি।
বেশ গুছিয়ে গাছিয়ে, চাপাচাপি দিয়ে একটা চিঠি লিখলেন উমাশশী বড় মেয়েকে। চিঠি লিখে জবাবের আশায় বসে থাকলেন।
এমন সময় একটা চিঠি এল সরাসরি উমাশশীর নামে। এ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত। উমাশশী আশাও করেননি, তাঁর নামে কর্তার চিঠি আসবে! যে-মানুষ গৃহত্যাগের সময় স্পষ্ট করে জানিয়ে গেছে, ইহকাল আর পরকাল—কোনো কালেই যেন স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ না হয়, সেই মানুষ লিখবে চিঠি!
ছেলেই চিঠি এনে মা’র হাতে দিল।
উমাশশী চিঠিটা হাতে নিয়ে প্রথমটায় বুঝতে পারেননি। পরে বুঝলেন। খামের ওপর উমাশশীর নাম লেখা। এতকাল ছেলেমেয়েদের নাম থাকত, এই প্রথম উমাশশীর নাম।
চা খাচ্ছিলেন উমাশশী। চিঠিটা উলটে পালটে দেখলেন। খামের মুখ বন্ধ। একটু ভারী ভারী লাগল।
উমাশশীর মুখে এতদিন পরে এই প্রথম চাপা হাসি ফুটল। কর্তার তেজ তা হলে ফুরিয়েছে। দিন দশ পনেরোর মধ্যেই তেজ ফুরোবার কথা, সে-জায়গায় প্রায় মাস পুরতে চলল, একটু বেশি তেজ দেখালেন এই যা!…তা হয়েছেটা কী? অর্শ চাগালো, না চাল কলা খেতে খেতে মাথা ঘুরে পড়েছেন কোথাও? নাকি হাত-পা ভেঙে পড়ে আছেন কোনো ডেরাভাণ্ডায়।
উমাশশী উঠলেন। পান মুখে দিয়ে সোজা ঠাকুরঘরে। নারায়ণকে একবার প্রণাম সেরে, চিঠিটা ঠাকুরের পায়ে ছুঁইয়ে ফিরে এলেন নিজের ঘরে। যে-মানুষ ঘর সংসার, স্ত্রী-পুত্র ফেলে পালায় তার খানিকটা শিক্ষা হওয়া উচিত। ভগবান যেন শিক্ষাটা ওকে দেন। উমাশশীকে আজ কতদিন নাকের জলে চোখের জলে করেছেন গুপ্তবাবু, সারারাত একরকম জাগিয়ে রেখেছেন—তার শাস্তি তাঁর পাওয়া দরকার। অবশ্য উমাশশী চান না, তার শাস্তিটা খুব ভারী কিছু হোক, অসখু-বিসুখ করে পড়ে থাকেন বেজায়গায়। ভগবানের কাছে সে-প্রার্থনাও তিনি জানিয়েছেন।
নিজেই চশমা নিয়ে চোখে দিলেন উমাশশী। তারপর খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠিটা বার করলেন।
না, কোনো ঠিকানা নেই, নিজের পাত্তা দেননি।
উমাশশী চিঠিটা পড়তে লাগলেন। কর্তা হরিদ্বার হৃষিকেশের দিকে চলে গেছেন।
হরিদ্বার, লছমনঝোলা উমাশশীর দেখা। একবার ছেলেবেলায় গিয়েছিলেন মা বাবার সঙ্গে। দ্বিতীয়বার যান স্বামীর সঙ্গে। চাকরি থেকে রিটায়ারের আগে স্বামী সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। বড় ভাল লেগেছিল। কর্তা বলেছিলেন, মেয়েদের বিয়ে থা হয়ে গেলে ঝাড়া হাত-পা হয়ে দুই বুড়ো বুড়ি মিলে এখানে এসে ডেরা বাঁধব, কি বল উমা?
কর্তা সেই হরিদ্বারের দিকেই গেছেন। অবশ্য সেখানেই থাকেননি, চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে হৃষিকেশ ছাড়িয়ে কোনো চটি টটিতে গিয়ে থেমেছেন।
কিন্তু কর্তার চিঠির সুরটাই যে বেখাপ্পা। এ-সব তিনি কি লিখেছেন:
“তোমায় পত্ৰ দিবার প্রয়োজন আমার ছিল না। বাধ্য হইয়া দিতেছি। সাংসারিক নিয়মে এবং আইনসঙ্গত ভাবে আমি তোমার স্বামী। যে-যাবৎ জীবিত থাকিব, স্বামী বলিয়াই গণ্য হইব। কিন্তু ধর্মত বলিতেছি, আমার স্বামীত্বে সাধ নাই, গৃহ সংসারেও বিন্দুমাত্র রুচি নাই। আমি এই অল্প সময়ের মধ্যে নিজেকে যেন ক্রমে ক্রমে চিনিতেছি। একটি বিরাট কুয়াশার জাল ছিন্ন হইয়া আমার সেই জন্মজন্মান্তরের রূপটি দেখা দিতেছে। এই রূপ হইবার কথা নয়। ঈশ্বর আমায় কেন জানি এই মহারহস্যের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া দিয়াছেন। ভগবানের মতি, আমি সামান্য মানুষ, কী বুঝিব। তবু বুঝিতে পারিতেছি—ওই যে যোগিনী, উহার সহিত কিসের এক নিগূঢ় সম্বন্ধে যেন আমি বাঁধা পড়িতে যাইতেছি। উনি কে, আমি কে? আর তুমি, যে-তুমি আমায় তিরিশ বৎসর অধিকার করিয়া রাখিয়াছিলে—তুমিই বা কে? আমার এইরূপ সন্দেহ জন্মিতেছে, তুমি ঠিকানা ভুল করিয়াছ। তোমার পিতামহাশয় ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন না, হিন্দুধর্মের মর্মটুকু তাঁহার মগজে প্রবেশ করে নাই। তিনি যদি ঠিকুজি কোষ্ঠী, গণনা ইত্যাদি মান্য করিতেন তবে, তোমার বা আমার ঠিকানা ভুল করিয়া একই স্থানে হাজির হইবার কথা নয়। তোমার যে কী মারাত্মক ভুল হইয়াছে তাহা তুমি জান না। আমিও জানিতাম না। সম্প্রতি জানিলাম। যোগিনী আমায় জানাইয়া দিলেন।
“এই যে যোগিনীর কথা লিখিতেছি ইনি নিজে একটি দুটির বেশি কথা বলেন না। লোকমুখে শুনিলাম, যোগিনী বিরাট বংশের মেয়ে, উচ্চশিক্ষিতা, অল্প বয়সেই ইঁহার মতিগতি অন্যপ্রকার হইয়া যায়। মাঝে মাঝে মূর্ছা যাইতেন। মূর্ছা ভাঙিলে কিছুক্ষণ ভাসা ভাসা এমন সব কথা বলিতেন যাহার অর্থ কেহ বুঝিতে পারিত না। বৎসর কয় পরে ইনি বলিতে লাগিলেন যে, তাঁহার পূর্বজন্মের কথা মনে পড়িতেছে। কেহ বিশ্বাস করিত না। শেষে দুই চারিটি প্রমাণ দিবার পর বাড়ির লোকজন বিশ্বাস করিল উনি জাতিস্মর। …যুবতী বয়সেই তিনি গৃহত্যাগ করিলেন। শুনিলাম উনি মানস সরোবরের দিকে কোথাও গিয়া দুই তিন বৎসর ছিলেন। একেবারে একা। সেখানেই যোগসাধনা করিতেন। হালে পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া এখানে একটি কাঠের ঘর নির্মাণ করিয়া আছেন। তাঁহার একজন অনুচর আছে। সে নদী হইতে জল আনে, ফলমূল চাল ডাল যাহা পায় জোগাড় করে, চুল্লি ধরায়। যোগিনী নিজে নিত্য আহার করেন না। কোনো কোনোদিন দু’ গণ্ডুষ জলই তাঁহার আহার।
এখানকার লোকে যোগিনীকে রাধামাঈ বলে। বয়েস তো বেশি নয় চল্লিশও হইবে না। কিন্তু দেবীর মতন চেহারা। রংটি তপঃপ্রভাবে উজ্জ্বল তামাটে, মাথার চুল পায়ে আসিয়া নামিয়াছে, নাক চোখ প্রতিমার মতন। গেরুয়া শাড়ি পরনে। গলায় রুদ্রাক্ষ মালা।
রাধামাঈ সর্বজ্ঞ। তিনি মানুষ দেখিলেই তাহার ভূত ভবিষ্যৎ জানিতে পারেন। আমি গতকাল সন্ধ্যার দিকে তাঁহাকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার দিকেই যাইবার নির্দেশ ছিল।
রাধামাঈয়ের বাহির কক্ষে একটি শতরঞ্জি বিছানো ছিল। সামনে বাঘছালের আসন। সম্ভবত কর্পূর ও ধূপ পড়িতেছিল। সামান্য ধোঁয়ার সহিত ক্ষুদ্র কক্ষটিতে ধূপের গন্ধ ছড়াইয়া রহিয়াছে। আমি একা বসিয়াছিলাম। এমন সময় যোগিনী আসিলেন। আহা, কী রূপ। কী অসামান্য লাবণ্য। কক্ষটি যেন হঠাৎ গন্ধে ভরিয়া গেল। তিনি দাঁড়াইয়া রহিলেন। আমায় একদৃষ্টে দেখিতে ছিলেন। দেখিতে দেখিতে অস্পষ্ট স্বরে কি যেন বলিলেন।
শুনিলে অবাক হইবে, তিনি আসনে বসিলে আমি ভক্তিভরে করজোড়ে তাহাকে নমস্কার জানাইয়া পরে প্রণাম করিতে গেলেই তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। একটি কুপির আলো জ্বলিতেছিল। আমি অবাক, অপ্রস্তুত। কখন যেন আমিও তাঁহার মুখোমুখি দাঁড়াইয়া পড়িলাম। তিনি নিষ্পলকে আমায় দেখিতে লাগিলেন। সেই দৃষ্টিতে কী ছিল আমি জানি না। আমার ভয় হইতে লাগিল, ঘন ঘন কম্পন লাগিল, কপালে গায়ে দরদর করিয়া ঘাম ছুটিল। তিনি নিশ্চল। আমার যেন সম্বিৎ লোপ পাইল। বঙ্কিমবাবুর সেই কপলাকুণ্ডলাকে যেন সাক্ষাৎ দেখিলাম।
শুনিলাম তিনি বলিতেছেন, ইয়ে কোন্ হ্যায়?
যোগিনী চলিয়া গেলেন। আমি বেহুঁশ হইয়া মাটিতে বসিয়া পড়িলাম।
ফিরিবার সময় রাধামাঈয়ের অনুচর আমায় বলিল, মাতাজি আমায় আগামী পূর্ণিমার দিন যাইতে বলিয়াছেন। তিনি আমার প্রণাম গ্রহণ করিতে পারেন না, মাতাজি ডাকটিও তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছে। কেন যে তাহা অনুচরটি জানে না। এরকম ঘটনা কখনো ঘটে নাই।
পরদিন দুপুরে রাধামাঈয়ের অনুচরটি আবার আসিল। আসিয়া জানাইল, মাতাজি বলিয়াছেন—আমার এই জন্মের সংসার জীবনে এক মায়াবিনী দূর স্থানে বসিয়া আমায় নাকাল করিবার ফন্দি আঁটিতেছে। তাহার ঘরে আমার ছবি, খাট বিছানা, জামাকাপড় সবই পড়িয়া আছে। এই সংসারের সামগ্রীগুলি লইয়া সে তুকর্তাক করিতেছে। যে-যাবৎ সে সমস্ত কিছু বাহিরে ফেলিয়া না দেয়—আমার যথার্থ পরিচয় প্রকাশ হইবার উপায় নাই। তুমি যে এখনও পিছন হইতে এমন করিয়া আঁকসি দিয়া টানিতেছ তাহা আমি কল্পনা করিতে পারি না। অনেক জ্বালা সহিয়াছি, আর কেন জ্বালা দাও? তোমার পায়ে ধরি, আমায় মুক্তি দাও।
জানি না, আগামী পূর্ণিমায় আমার কোন অভিজ্ঞতা হইবে।”
উমাশশী চিঠিটা রেখে দিলেন। মনের মধ্যে হু হু করতে লাগল। কে সেই যোগিনী? কেন তার অমন রূপ? কর্তা বলেছেন দেবীর মতন রূপ। কর্তা যতই দেবী দেবী করুন উমাশশী মোটেই দেবীতে ভুলবেন না। যোগিনী কেন প্রণাম নিল না কর্তার। সে নাকি জাতিস্মর, পূর্বজন্মের কথা জানে। এখানেই উমাশশীর বড় খটকা। যে যোগিনী শয়ে শয়ে লোকের প্রণাম নেয়, সে কেন তার প্রণাম নেবে না। তবে কি কার্তার প্রণাম নেবার অধিকার তার নেই। কেন? কোন দরকারে আবার পূর্ণিমার দিন যেতে বলেছে কর্তাকে?
উমাশশীর ভয় হচ্ছিল। যোগিনীরা অনেক কিছু পারে। তাদের অসাধ্য কিছু নেই। বুড়ো কর্তাকে তারা ছাগল ভেড়াও করে দিতে পারে। নিকুচি করেছে তোর কপালকুণ্ডলার।
কি যে করবেন উমাশশী কিছু বুঝতে পারলেন না। উঠলেন। পান খেলেন। বাতিটা নিবিয়ে দিলেন। বাইরে বেশ চাঁদের আলো। কাছেই পূর্ণিমা। হায় হায়, পূর্ণিমার দিন তাঁর কী সর্বনাশ হবে কে জানে।
উমাশশী হঠাৎ গলায় আঁচল জড়িয়ে ঠাকুর দেবতার পায়ে মাথা কুটতে কুটতে মানত করলেন, হে ঠাকুর তুমি কর্তাকে যেতে দিও না। কিছু একটা করে দাও ওঁর, যাতে বিছানা ছেড়ে উঠতে না পারে। হাত পা মচকে দাও, কোমরে ফিক ব্যথা ধরিয়ে দাও, না হয় কাবু করে দাও অর্শে। আমায় বাঁচাও।
নাটকে যেমন পট পরিবর্তন, সিনেমায় কলকাতা থেকে কার্শিয়াঙে গমন—সেই রকম এই কাহিনীর স্থান কাল পাত্রের কিছু পরিবর্তন ঘটল।
স্থানটি নিরিবিলি। কাছকাছি শালের পাতলা জঙ্গল। ছোট মতন এক বাংলো বাড়ি, সামনে দিয়ে কাঁচা রাস্তা চলে গেছে পশ্চিমে। দু’ চারটে ইউক্যালিপটাস গাছও চোখে পড়ে বাংলোর কাছে। সময়টি শেষ বিকেল। এই মাত্র সূর্য ডুবল।
বাংলোর ঢাকা বারান্দায় তিন চারটি বেতের চেয়ার পাতা। একটি গোল বেতের টেবিল। চা খাওয়া শেষ হয়েছে, টেবিলের ওপর চায়ের পট, শুন্য কাপ, দুধ চিনি পাত্র, বিস্কিটের প্লেট পড়ে আছে। এক মহিলা এবং দুই ভদ্রলোক বসে আছেন চেয়ারে। দুই ভদ্রলোকের একজন সারদা গুপ্ত—উমাশশীর স্বামী। অন্যজন সারদা গুপ্তের ভায়রাভাই। নিজের নয়, সামান্য দূর সম্পর্কের। নাম পরিমল। মহিলা অবশ্যই সারদা গুপ্তের শ্যালিকা। নাম রেবা। উমাশশীর এক মাসির মেয়ে, কাজেই মাসতুতো বোন।
সারদা গুপ্ত চায়ের পর সিগারেট খাচ্ছিলেন, হাতে-পাকানো সিগারেট। চেহারাটি মন্দ নয়। এই বয়সেও শক্ত সমর্থ, গায়ের রং পরিষ্কার। মুখটি হাসিখুশি। মাথার চুল প্রায় সাদা হয়ে গেছে। পরিমল বয়েসে বেশ কিছু ছোট, বছর আটচল্লিশ হতে পারে। ছিপছিপে গড়ন। সরল চেহারা। রেবার বয়েস চল্লিশ-টল্লিশ হবে, সুশ্রী মুখ, নরম ধাতের ছাঁদ। নাকটি মোটা চোখ দুটি ডাগর।
পরিমল এবং রেবা কিছুক্ষণ সন্তর্পণে নিজেদের মধ্যে চোখ চাওয়া চাওয়ি করছিল। যেন কিছু বলার আছে বলতে পারছে না। এমন সময় এঞ্জিনের হুইসল বাজিয়ে দূর দিয়ে একটা মালগাড়ি গোছের কিছু চলে গেল। পরিমল হুইসলের শব্দে রীতিমত ঘাবড়ে গেল, তাকাল স্ত্রীর দিকে। রেবা চোখে চোখে ইশারা করল কিছু।
পরিমল সারদা গুপ্তের দিকে তাকাল। ইতস্তত করল খানিকটা। তারপর বলল, “সারদাদা একটা—মানে একটা ব্যাপার হয়ে গেছে।”
“ব্যাপার?” সারদা বেশ আলসেমির চোখে ইউক্যালিপটাস গাছের নাচন দেখছিলেন। শীত আসি-আসি ভাব। বাতাস রয়েছে এলোমেলো। আকাশে আলো নেই। ঝপ করে অন্ধকার নেমে আসবে একটু পরেই। ভায়রার দিকে চোখ ফেরালেন সারদা। “ব্যাপার! কী ব্যাপার হে?”
পরিমল গলা ঝাড়ল, সোঁ সোঁ করে বার দুই নিঃশ্বাস টানল, তারপর অপরাধীর মতন করে বলল, “আজ সন্ধের ট্রেনে ইয়ে আসতে পারেন।”
“ইয়ে! ইয়েটা আবার কে?”
পরিমল তার গলার কাছটা চুলকোতে লাগল। জড়ানো গলায় বলল, “দিদি।”
“দিদি? কোন দিদি?”
“বড়দিদি—মানে উমাদিদি!”
সারদা গুপ্তকে যেন বিছেয় কামড়াল। লাফ মারলেন না, কিন্তু তাঁর চোখমুখ নীলচে হয়ে গেল। একেবারে স্তম্ভিত। গলায় ঘড়ঘড় শব্দ হ’ল একটু। তারপর বললেন, “আমায় ভয় দেখাচ্ছ! তোমার বড়দিদি এখানে আসবে? কেমন করে আসবে?”
পরিমল একবার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে সাহস সঞ্চয় করে নিল যেন, বলল “আসারই তো কথা। আমরা সন্ধের ট্রেনে দিদিকে এক্সপেক্ট করছি।”
বিশ্বাস করলেন না সারদা। মাথা নাড়লেন জোরে জোরে। “ধ্যুত, অসম্ভব। তোমার দিদি আমার ঠিকানা পাবে কোথায়! আমি তো এখন বিন্ধ্যটিন্ধ পেরিয়ে কোথায় চলে গেছি। হিমালয়ে। গঙ্গোত্রীর পথ ধরেছি। এক একটা ডোজ যা দিচ্ছি তোমার দিদিকে—উমারাণীর মাথায় চক্কর মারছে। মহিলাকে ম্যাপ খুলে বসে ট্রেস করতে হচ্ছে আমি কোথায়, হৃষিকেশে না কোনো হিমবাহতে। কিস্যু বুঝতে পারছে না। আমি বাজি ফেলতে পারি।”
পরিমল বলল, “কিন্তু একটা ব্যাপার যে হয়ে গেছে।”
“আবার ব্যাপার? কত ব্যাপার হবে তোমার?”
“কাল আমি একটা টেলিগ্রাম করেছি তপুকে। আজ সকালে নিশ্চয় পেয়েছে। আশা করছি বিকেলের ট্রেনে দিদিকে নিয়ে তপু এসে পড়বে।”
সারদা যেন চেয়ার ভেঙে মাটিতে পড়ে গেলেন এই রকম ভাব করলেন, অবাক, বিহ্বল, নির্বাক। হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন ভায়রার মুখের দিকে। “তুমি টেলিগ্রাম করলে?”
“আপনার শালী বলল।”
সারদা রেবার দিকে তাকালে। খুবই পছন্দ করেন শালীটিকে। যত্ন করেন।
রেবা বলল, “সবটাই আমি বলিনি জামাইবাবু, আপনার ভায়রাও বলেছে।”
“কেন?” সারদা শালীর দিকেই তাকিয়ে থাকলেন।
রেবা বলল, “আপনি রাগ করবেন না জামাইবাবু, আমি অন্যায় কিছু করিনি। আজ ক’দিন আপনার শরীর মোটেই ভাল যাচ্ছে না।”
“কে বলল ভাল যাচ্ছে না। খাচ্ছি, দাচ্ছি বেড়াচ্ছি। তোমাদের সঙ্গে গল্প করছি। হাতের কাছে বই পেলে পড়ছি। এর চেয়ে আর কী ভাল যাবে।”
মাথা নাড়ল রেবা। বলল, “না জামাইবাবু, আপনি প্রথম প্রথম এসে দিন সাতেক বেশ ফুর্তিতে ছিলেন। খাওয়া দাওয়া করেছেন। রাত্রে ঘুমোতেন। কিন্তু আস্তে আস্তে আপনার খাওয়া দাওয়া কমেছে। মুখে অরুচি এসেছে। রাত্রে ঘুমোতে পারেন না ভাল। আমরা তো পাশের ঘরে থাকি—রাত্রে আপনি চার পাঁচবার করে ওঠেন। বাথরুমে যান। ঘরের মধ্যে খুটখাট করেন। সকালের দিকে আপনাকে দেখলে বোঝা যায়, যেটুকু ঘুমিয়েছেন, তাও শান্তিতে নয়।”
“এ সবই ছুতো,” সারদা বললেন, “আমি ঠিকই ছিলাম, ঠিকই আছি। তোমরা আমার সঙ্গে শত্রুতা করলে; সেরেফ বেইমানি। যদি এই তোমাদের মনে ছিল, তা হলে আমি যখন লিখেছিলাম—কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে চাই, জায়গা হবে?—তখন তো বাপু বলে দিলেই পারতে সোজা কথাটা।”
পরিমল ভীষণ অপরাধীর মতন মুখ করে বসে থাকল! রেবা বোঝাতে লাগল সারদাকে। বলল, “ছি জামাইবাবু, কি যে বলছেন আপনি! আমরা তো এখানে বদলি হয়ে মাত্র দু’তিন মাস এসেছি। আপনাকে ছাড়া বড় কাউকে খবর দেওয়াও হয়নি। আপনার ভায়রা তো জঙ্গলে সারভে আর নকশার কাগজপত্র নিয়ে দিন কাটায়। আপনি আসবেন শুনে পর্যন্ত আমরা নাচতাম।”
“নাচতে বইকি! আমায় ভুলিয়ে ভালিয়ে এনে আমায় নাচাবার জন্যে নাচতে—” সারদা বললেন। মুখ গম্ভীর। যেন নাচানো পার্টির ফাঁদে পড়ে এখন তাঁর অনুশোচনা হচ্ছে।
পরিমল অপ্রস্তুত। স্ত্রীর দিকে তাকাল একবার। তারপর দুহাত জোড় করে মিনতি ভঙ্গিতে বলল, “দাদা, আপনার সঙ্গে আমাদের কি সেই সম্পর্ক! আপনার শালী আপনাকে কত খাতির করে, ভালবাসে, সে তো আপনি জানেন।”
“জানি হে, জানি। শালীর ভালবাসাও জানি, শালীর দিদির ভালবাসার ঘটাও জানি। এক জাতের মুরগি।”
রেবার হাসি পাচ্ছিল। হাসল না। সারদার দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, “মুরগির জাত যেমনই হোক জামাইবাবু, আপনি যদি আমায় অবিশ্বাস করেন, আমি আর কথাটি বলব না।” বলে একটু থেমে অভিমানের গলায় রেবা আবার বলল, “আপনি আসবেন শুনে আমরা কী আনন্দ পেয়েছি! এসে পর্যন্ত, বলুন, আমাদের কত আনন্দেই দিন কেটেছে।”
সারদা হাত তুলে থামিয়ে দিলেন রেবাকে। নিজেরই কেমন মনে হল। একটু কড়া কথা বলে ফেলেছেন। সামান্য চুপ করে থেকে বললেন, “যা করেছ, বেশ করেছ! কিন্তু ওই বাঘের মুখে এই অধমকে ঠেলে দিলে। এটা কেমন হল জানো, ছাগলের গলায় দড়ি বেঁধে বাঘকে নেমন্তন্ন করা। এখন আমি করব কী?”
রেবা হেসে ফেলেছিল। বলল, “বাঘকে আমরা সামলাব।”
“ও তোমাদের কর্ম নয়। বত্রিশ বছরে আমিই পারলাম না—তোমরা সামলাবে!…তা হ্যাঁ হে পরিমল, কী লিখেছ টেলিগ্রামে?”
“লিখেছি, সারদাদা সিরিয়াসলি ইল। কাম ইমিডিয়েটলি উইথ দিদি।”
“আমি ইল? অসুস্থ? সিরিয়াসলি অসুস্থ?…এসব কেন লিখলে? আমার চেহারাটা কি ইলের মতন দেখাচ্ছে? সর্বনাশ করলে তুমি হে! একেই তো মাত্র পনেরো মাইল দূরে পালিয়ে এসে বসে আছি; বসে বসে ব্লাফ ঝাড়ছি—হিমালয় টিমালয় পর্যন্ত চালিয়েছি চিঠিতে। তার ঠেলা সামলাতেই বাবার নাম ভুলে যাব। তার ওপর মুরগির আণ্ডা ওড়ানো, ঘি দুধ সেবন করা এই চেহারাকে ইল বলে চালানো কী সোজা কথা! তোমার দিদি কচি খুকি? ঝিনুকে দুধ খায়!…ওরে বাব্বা, এ কী সর্বনাশ করলে তোমরা! ডবল ব্লাফ! আমার মাথার চুল উপড়ে ফেলবে তোমার দিদি। পরিমল, আমায় বরং এখানে সমাধি দিয়ে দাও।”
রেবা জোরে হেসে ফেলল। পরিমলও।
পরিমল বলল, “বাঃ অসুখ হতে পারে না। আপনার অসুখ হয়েছে।”
“কী অসুখ?”
কী অসুখ? পরিমল ঝঞ্চাটে পড়ে গেল। কোন অসুখ করবে সারদাদার?
কোন অসুখ? পাঁচ সাতটা অসুখের নাম যেন এর ওর গায়ে জড়িয়ে ফাঁদে লেগে গেল। ঝট করে একটা নামও পড়ে পড়ল না। তারপর ঝপ করে নিওমোনিয়া-র নামটাই মাথায় এল। পরিমল বলল, “নিওমোনিয়া।”
“নিওমোনিয়া!…তুমি মুখে বললে আর নিওমোনিয়া হয়ে গেল। অত সহজ ব্যাপার! হাই টেম্পারেচার, বুকে কনজেসান, দু’চারটে বুক ফাটানো কাশি—এসব পাব কোথায়!” সারদা বললেন।
পরিমল ফাঁপরে পড়ল। কানের ডগা চুলকে বলল, “জণ্ডিস হতে পারে না?”
সারদা নিজের চোখ দেখালে। “আমার চোখ কি হলুদ? গা ফ্যাকাশে? ন্যাবা আরও ডিফিকাল্ট।”
পরিমল স্ত্রীর দিকে তাকাল। রেবা দুচারটে অসুখের নাম করল, ছোটখাটো অসুখ, ডায়েরিয়া ডিসেন্ট্রি গোছের। তাতে সারদা খুশি হলেন না। লিখেছ ‘সিরিয়াসলি ইল’, এখন বলছ ডায়েরিয়া। রসিকর্তা নাকি?
সারদা বললেন, “একটা আজেবাজে ছুতো করে ডেকে পাঠালে তোমাদের দিদি কী ভাববে, বুঝতেই তো পারছ। ভাববে কলকাঠিটা আমিই নেড়েছি। আমার ইজ্জত তো যাবেই, তোমাদেরও রক্ষে রাখবে না।”
রেবা বলল, “আমাদের ওপর বড়দি এমনিতেই রেগে আগুন হয়ে গিয়েছে। আপনি এত দিন ধরে রয়েছেন এখানে। আমরা কেন কিছু জানাইনি।”
“তোমাদের ওপর রাগবে কেন—” সারদা বললেন, “তোমরা বলবে, জামাইবাবু বাড়িতে রেগুলার চিঠি লেখেন, আমরা কেমন করে বুঝব, তিনি কিছু লুকিয়ে রাখছেন।”
রেবা বলল, “দিদিকে অত সহজে বোঝানো যায়! ঠিকই বুঝে নেবে—সবই ষড়যন্ত্র।”
পরিমল বার বার ঘড়ি দেখছিল। ঝাপসা অন্ধকারে চাঁদ উঠেছে। বলল, “আমি আর দেরি করব না। স্টেশনের দিকে এগোই।”
সারদা বললেন, “তা তো এগুবে। কিন্তু আমার কী হবে?”
পরিমল উঠতে উঠতে বলল, “আমি স্টেশন থেকে দিদিকে ম্যানেজ করতে করতে আসব। বলব, হঠাৎ খুব বাড়াবাড়ি হয়েছিল, আমরা ভয় পেয়ে টেলিগ্রাম করেছিলাম। সারদাদা এখন ভাল। কোনো ভাবনা নেই আর!”
সারদা যেন বিরক্ত হয়ে বললেন, “তোমার মতন হাঁদা আমি আর জীবনে দেখিনি। তোমার দিদিকে না হয় বললে বাড়াবাড়ি হয়েছিল, কিন্তু কিসের বাড়াবাড়ি, তা বলতে হবে না? বাড়াবাড়িটা কিসের? কোন রোগের?”
পরিমল বলল, “ম্যালেরিয়া। এই বনজঙ্গল জায়গা। এখানে মশাটশা খুব। হঠাৎ ম্যালিগনান্ট টাইপের ম্যালেরিয়া হয়ে গিয়েছিল, একশো তিন চার জ্বর। ভীষণ কাঁপুনি। বিকার।…সে আমি ম্যানেজ করে বলে দেব।”
“ও-রকম বিকট ম্যালেরিয়াটা গেল কোথায়?” সারা জিজ্ঞেস করলেন।
“জ্বরটা ছেড়ে গেছে। কাল রাত্রে, কিংবা আজ সকালে।…ম্যালেরিয়ার জ্বর যখন তখন ছাড়তে পারে। কারও কিছু বলার নেই।”
“কী মুশকিল!” সারদা বললেন, “আমার চেহারাটাকে তো ম্যালেরিয়া রোগীর মতন করতে হবে। চকচক করছে চেহারা, কামানো মুখ, মাথায় জবাকুসুমের গন্ধ…। এখানে ম্যালেরিয়াকে আমদানি করবে কেমন করে! তুমি কনসিকুয়েন্সটা একেবারে বুঝতে পারছ না, পরিমল। তোমার দিদি পুলিশের মেয়ে, ওদের রক্তের মধ্যে সন্দেহ। অত সস্তায় শ্রীমতী উমাশশী গুপ্তকে ভোলানো যাবে না।”
পরিমল সমস্যায় পড়ল। সময় হয়ে আসছে। তাকে স্টেশনে যেতেই হবে। কম করেও মিনিট পনেরোর পথ। জিপ গাড়িটা খারাপ হয়ে পড়ে আছে, নয়ত গাড়ি নিয়ে চলে যেত।
পরিমল বলল, “কিন্তু আমায় তো যেতে হবে। ট্রেনের টাইম হয়ে আসছে।”
রেবা কিছু ভাবছিল চুপচাপ। হঠাৎ মুখ তুলে বলল, তুমি যাও, আর দেরি কোরো না। আসার সময় একটা কিছু যোগাড় করে নিও। দিদিকে হাঁটিয়ে এনো না। হাঁটতে পারবে না ও।”
সারদা বললেন, “গড়িয়ে এনো।”
রেবা হেসে ফেলল। পরিমলকে বলল, “অসুখের কথা—মানে কী হয়েছিল তোমায় বলতে হবে না। বোলো, শরীরটা জামাইবাবুর খুব খারাপ হয়েছিল। এখানে ভাল ডাক্তার নেই। যাকে ডেকে দেখানো হয়েছিল, তিনি বলেছেন—হার্টের অসুখ।”
পরিমল একবার সারদার দিকে তাকাল।
সারদা যেন হাল ছেড়ে দিয়েছেন। বললেন, “তাই বোলো। হার্ট তো দেখা যায় না, ওটাই যা ভরসা।”
পরিমল ঘরের দিকে চলে গেল। হয়ত জামা পালটাতে, জুতো জোড়া পরে নিতে।
সারদা সিগারেটা আবার ধরিয়ে নিলেন।
একটু পরেই পরিমল বেরিয়ে এল। বলল, “আমি তা হলে আসছি।” বলে সে গেটের দিকে চলে গেল।
রেবা চায়ের পাত্র গুছিয়ে নিতে লাগল।
সারদা সামনের দিকে তাকিয়ে খুব পরিষ্কার চাঁদের আলো দেখতে পেলেন। এতক্ষণ ঠিক লক্ষ করেননি। বললেন, “আজই কি পূর্ণিমা?”
রেবা চাঁদের দিকে তাকাল। বলল, “বোধ হয়। গতকালও চাঁদটা এই রকম ছিল।”
সারদা বললেন, “পৃর্ণিমায় আমার যে যোগিনী রাধামাঈয়ের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা ছিল।” বলে বেশ বড় করে নিঃশ্বাস ফেললেন সারদা।
“সে আবার কে?” রেবা জিজ্ঞাসা করল।
সারদা বললেন, “সে হল সাক্ষাৎ মোহিনী, যোগিনী, জাতিস্মর। অপরূপ-লাবণ্যময়ী কামিনী। বয়স চল্লিশের স্লাইট এপারে। আমার জন্মজন্মান্তরের গাঁটছড়া। তোমার দিদিকে ওটা লেটেস্ট দিয়েছিলুম। ওতেই উমারাণী কাত হয়ে পড়তেন। হচ্ছিলেনও একটু একটু, তোমরাই সব গণ্ডগোল করে দিলে।”
রেবা মুচকি হাসল। চায়ের পাত্র গুছিয়ে নিয়ে উঠতে উঠতে বলল, “আপনার ঘরে বিছানাপত্তর ঠিক করে দিচ্ছি। খানিকটা পরে গিয়ে শুয়ে পড়বেন। আপনি কিন্তু হার্টের রোগী।” বলে হেসে উঠল!
সারদা বিছানায় শুয়েই ছিলেন। বড় বড় দুটো জানলার একটিমাত্র খোলা। ঘরে আসবাবপত্র বেশি নেই। সারদার খাটটিও ছোট, একার মতন। ঘরের কোণের দিকে কেরোসিনের টেবিল বাতি জ্বলছে। এখানে ইলেকট্রিক নেই। গায়ে একটা মোটা কম্বল চাপিয়েছেন সারদা। রেবা চাপিয়ে দিয়ে গেছে। কম্বল না চাপালে নাকি অসুখ-অসুখ দেখায় না। সারদা এই সন্ধেবেলা কম্বলচাপা হয়ে ঘামছিলেন। ঘামটা তাঁর ভাল লাগছিল না। কিন্তু হার্টের রোগী হিসেবে এটা সহ্য করছিলেন। মুখটা তাঁর এতই পরিষ্কার যে কিঞ্চিৎ মলিন না করলে চলছিল না বলে সারদা সামান্য পাউডারের সঙ্গে কাগজ-পোড়া ছাই মিলিয়ে মুখে মেখে নিয়েছেন পাতলা করে। উপায় নেই। শুয়ে শুয়ে বোধ হয় তিনি ভগবানের নাম জপছিলেন।
এমন সময় গাড়ির শব্দ। সারদার বুক কেঁপে উঠল। উমা কি এসেছে? না আসেনি?
সামান্য পরেই গলার আওয়াজেই বোঝা গেল, উমাশশী ছেলেকে নিয়ে হাজির হয়েছেন। সারদার বুক ধকধক করতে লাগল, গলা কাষ্ঠবৎ, গলগল করে ঘামতে লাগলেন। ছেলেবেলায় বলির পাঁঠা সম্পর্কে তাঁর যত মমতা ছিল নিজের ওপর তার চেয়েও বেশি মমতা হচ্ছিল। বলির পাঁঠা হতভাগ্য জীব, কিন্তু মানুষ আরও হতভাগ্য, পাঁঠার স্ত্রী থাকে না, মানুষের থাকে। অন্তত সারদার রয়েছে।
দরজায় পায়ের শব্দ। সারদা চোখের পাতা বুজে ফেললেন। জিব গলার দিকে টানতে লাগল। বুক আওয়াজ মারছে, নিজের কানেই শুনতে পাচ্ছিলেন সারদা।
চোখ বন্ধ করেই সারদা বুঝলেন ঘরে উমাশশী, রেবা, পরিমল আর তপু এসে দাঁড়িয়েছে। আস্তে গলায় কথা বলছিল রেবা। “ডাক্তার বলেছেন, একেবারে চুপচাপ শুয়ে থাকতে। সাড়াশব্দ যেন না হয়। যত ঘুম হয় ততই ভাল। জামাইবাবু প্রথম দিকে বেশ ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন। কাল রাত থেকে ভাল। আজ সকালে দু’ একবার বিছানায় উঠে বসেছিলেন। বিকেলে চা খেয়েছেন। এখন বোধ হয় ঘুমোচ্ছেন। ডাকব!
“থাক, তোকে ডাকতে হবে না, আমি দেখছি…” বলে উমাশশী বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালেন।
সারদা চোখ বুজেই থাকলেন। কম্বলের তলায় হাত পা কাঁপছিল।
“আলোটা একবার আন তো,” উমাশশী বললেন, বলে বিছানায় বসতে গেলেন, কুলোতে পারলেন না, কোনোরকমে বসলেন। কপালে হাত দিলেন সারদার, বুকে হাত রাখলেন।
পরিমল আলো হাতে এসে দাঁড়াল। বোধ হয় আসার সময় পলতেটা আরও কমিয়ে দিয়েছিল। তার হাতও কাঁপছে।
উমাশশী স্বামীর মুখের ওপর আরও ঝুঁকে পড়ে কী দেখলেন। নিবিষ্ট চোখে। তারপর বললেন, “বড্ড ঘেমেছে। কম্বলটা চাপিয়ে দিয়েছিস কেন? জানলা খুলে দে।” নিজের হাতেই কম্বল সরিয়ে দিলেন উমাশশী। রেবা জানলা খুলে দিল।
উমাশশী বললেন, “তোয়ালে-টোয়ালে দে একটা, ঘামটা মুছিয়ে দি। এত ঘাম গায়ে জমলে সর্দিকাশি হবে।” বলেই কি খেয়াল হল, আবার বললেন, “আচ্ছা থাক, আমি হাত পায়ে জল দিয়ে কাপড় চোপড় ছেড়ে এসে বসছি, তারপর যা করতে হয় করব।”
রেবা বলল, “সেই ভাল। চলল, তুমি কাপড় ছেড়ে একটু চা খেয়ে নাও। জামাইবাবুর ঘুমটা ভাঙুক।”
উমাশশীরা চলে গেলেন। পরিমল শুধু দাঁড়িয়ে থাকল।
সারদা খুব সাবধানে চোখে খুললেন। তারপর পরিমলকে বললেন, “কী বলল হে?”
“কিছু না।”
“সেকি! স্টেশন থেকে এতটা পথ এল, কিছু বলল না?”
“অসুখের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।”
“তুমি হার্ট ট্রাবল বলেছ তো?”
“বলেছি।”
“কেমন মনে হচ্ছে? ভয় পেয়েছে বুঝলে? ওয়ারিড?”
“তাই তো মনে হল।”
“…কোনো ফায়ারিং করল না?”
“কই! করল না!”
“খুবই আশ্চর্যের কথা।…দেখ কী হয়।…যাও, তুমি বাতি রেখে পালাও।”
পরিমল চলে গেল।
সারদা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভবিষ্যৎ-চিন্তা করতে লাগলেন। গিন্নির মতিগতি খানিকটা অন্যরকম মনে হচ্ছে। গলার স্বরটাও যেন নরম লাগল। কপালে বুকে হাত দেবার সময় হাতের চাপটি ভালই লেগেছিল। তা হলে কি শ্রীমতী উমাশশী একটু কাবু হয়ে পড়েছেন? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।
গা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে উমাশশী একবার স্বামীর বিছানায় এসে বসেছিলেন। সারদার গায়ের ঘাম তখন অনেকটাই শুকিয়ে গেছে। শাড়ির আঁচলে বুক মুছিয়ে দিলেন কর্তার। মুখটা। সারদা ঘুমের ভান করে চোখ বুজেই থাকলেন। কর্তার মুখ মুছিয়ে আঁচলটা কাঁধে ওঠাতেই কিসের গন্ধ মতন লাগল। গন্ধটা নাকের কাছে এনে শুঁকে নিলেন। সারদা বার দুই উঃ আঃ—করলেন ঘুমের ভানের মধ্যেই। উমাশশী কিছুই বললেন না। খানিকটা পরে উঠে বোনের কাছে চলে গেলেন।
অনেকক্ষণ থেকেই সারদা একবার ছেলেকে ডাকার ছুতো খুঁজছিলেন। পেরে উঠছিলেন না উমাশশীর ভয়ে। সুযোগ পেলেন আরও খানিকটা পরে। পরিমল মাঝে মাঝে তদারকি করতে আসছিল। অবশ্য ঠিক তদারকি নয়, উমাশশী আর রেবার মধ্যে যে সব কথা হচ্ছে, আড়ালে তার সমাচার জানাতে আসছিল। সারদা ভায়রাকে বললেন, “একবার তপুকে ডেকে দিতে পারো! বি ভেরি কেয়ারফুল।”
তপু একসময় চোরের মতন এসে ঘরে ঢুকল।
সারদা বললেন, “কিরে, পজিসন কী?”
তপু বলল, “তুমি খুব টাইমলি রিট্রিট করেছ। নয়ত কামানের গোলা খেতে। আমরা আর পজিসন ধরে রাখতে পারছিলাম না।”
সারদা বললেন, “আমার আরও একটা দুটো ফাইন্যাল অ্যাসাল্টের ইচ্ছে ছিল। তোদের মেসো মাসিই ডোবাল।”
তপু ফিসফিস করে বলল, “না না, আরও অ্যাসাল্ট হলে আমরা সরে যেতাম।” বলে তপু আর দাঁড়াল না। পালিয়ে গেল।
সারদার ভাল লাগছিল। তিনিই তো শেষ পর্যন্ত জিতেছেন। কিন্তু ভাল লাগাটা স্থায়ী হচ্ছিল না; ভয়ও হচ্ছিল। ভরসা পাচ্ছিলেন না। উমাশশীর সঙ্গে নিভৃত সাক্ষাতে তাঁর যে কী অবস্থা হবে, সে শুধু ভগবানই জানেন।
আসামাত্র স্বামীর সমস্ত কর্তৃত্ব উমাশশী নিজের হাতে নিয়ে নিয়েছিলেন। কাজেই রাত্রে সারদার চনচনে খিদে হওয়া সত্ত্বেও এক কাপ দুধ আর দুটো মামুলি বিস্কিট ছাড়া কিছু জুটল না। হার্টের অসুখে পেট হালকা রাখতে হয়, নয়ত গ্যাস উঠে বুকে ঠেলা মারবে। উমাশশীর বাবা হার্টের রোগেই মারা গিয়েছিলেন, তা ছাড়া কতই না শুনছেন তিনি।
রাত হল। সারদার খাটটা ছোট। উমাশশী নিজের শোবার জন্যে মেঝেতে কম্বল বিছিয়ে একটা বিছানা পেতে নিলেন। রেবা পরিমল অনেক আপত্তি করেছিল, উমাশশী শোনেননি। স্বামীর অসুখ, তাঁকে তো সারা রাত বসে বসেই কাটাতে হবে, নজর রাখতে হবে রোগীর ওপর, ওই একটা কম্বল মাটিতে পাতা থাকা—ওতেই হবে।
খাওয়াদাওয়ার পাট চুকে গেলে উমাশশী সারদার ঘরে এসে দরজায় ছিটকিনি তুলে নিলেন। পাশের ঘরটা রেবাদের। তার পাশে ছোট মতন বসার ঘর, তপুর বিছানা হয়েছে সেখানে।
ঘরে এসে উমাশশী আরও একটু জরদা মুখে দিলেন। বোধহয় আগেরটুকু কম হয়েছিল। বাতিটা কমিয়ে দিলেন। জানলা দুটো দেখলেন। ঠাণ্ডা আসছে সামান্য। মাথার দিকে জানালাটা ভেজিয়ে দিলেন। পাশের দিকেরটা খোলা থাকল। ঘরে চাঁদের আলো আসছে না, কিন্তু গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে আছে।
সারদার পেটে খিদে, অনেকক্ষণ সিগারেটও খেতে পারেননি, বেশ অস্বস্তি লাগছিল। তার ওপর উমাশশী ঘরে এসে ছিটকিনি তুলে দেবার পর থেকেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন।
উমাশশী হঠাৎ পা দিয়ে নিজের বিছানা গুটিয়ে দিলেন। দিয়ে সারদার বিছানার কাছে এসে বললেন, “মটকা মেরে অনেকক্ষণ পড়ে আছ। দেখাচ্ছি তোমায়। ওঠো।”
সারদা চোখ বুজে ছিলেন। আরও চেপে চোখ বুজলেন। কানে যেন শুনতে পাননি। ঘুমিয়ে রয়েছেন।
ঠেলা মারলেন উমাশশী। “ন্যাকামি হচ্ছে! বুড়ো ঘুঘু!”
সারদা আরও ঘাবড়ে গেলেন। বুঝতে পারলেন না, তাঁর হার্টের রোগটাকে আঁকড়ে থাকবেন, না বিসর্জন দেবেন। চোখ খুলে জড়ানো গলায় বললেন, “আঃ, কে? বুকের বাঁ দিকটায়…” বলে বাঁহাতে বুক চেপে ধরলেন।
উমাশশী খানিকটা ধাক্কা মেরেই স্বামীকে খাটের একপাশে সরিয়ে দিয়ে পাশে বসলেন। মাথায় কাপড় নেই, গায়ের আঁচলটাও বুকের তলায় নেমেছে।
সারদা বুঝতে পারলেন, আত্মরক্ষা না করলে অবধারিত পতন।
উমাশশী স্বামীর বুকে জোর একটা খোঁচা মারলেন, “এখনও ঢং করে চোখ পিটপিট করছ? তাকাও ভাল করে, নয়ত চোখ গেলে দেব।”
সারদা তাকালেন। বললেন, “আমার বুকে ব্যথা, খোঁচা মেরো না, মরে যাব।”
“তোমার বুকে আমি কিল মারব,” বলে উমাশশী সত্যিই মুঠো পাকালেন।
ভয়ে সারদা ধড়মড় করে উঠে বসলেন। হাত নয় তো হামানদিস্তে উমাশশীর, বার দুই বুকে পড়লে পাঁজরা ভেঙে যাবে। সারদা বললেন, “হচ্ছেটা কী? তুমি কি আমায় মারধোর করতে এসেছ?”
“কী করতে এসেছি, বোঝাচ্ছি তোমায়।…আগে বলো, নগদ চারশো টাকা কোথায়?”
সারদার সম্মানে লাগল। বললেন, “তোমার কাছে টাকার হিসেব দিতে হবে?”
“হবে।”
“আমার টাকা। আমি যা খুশি করব।”
“চেঁচামেচি কোরো না। আস্তে কথা বলল। ঘরে তোমার ডাকাত পড়েনি। বেহায়া মদ্দ!…আমার আলমারি ভেঙে সংসারের টাকা নিয়ে পালিয়ে এসেছ, চোর কোথাকার। আবার বলছ, তোমার টাকা!”
সারদা অশান্তি বাড়াতে চাইলেন না। বললেন, “টাকা ফেরত পাবে। গোটা পঞ্চাশ খরচ হয়েছে।”
“আংটিটা কোথায়?”
“আছে।”
“জামা, প্যান্ট, শাল সব আছে? না হারিয়েছ?”
“সব আছে। এদিক ওদিক পড়ে আছে। খুঁজে নাও গে যাও।”
উমাশশী কানই করলেন না, মুখটা বেঁকালেন। বললেন, “বুড়ো বয়েসে এই ঢং করবার কী দরকার ছিল?”
সারদা জবাব দিলেন না। রাগ, দুঃখ অভিমান, অপমান—সব যেন মনটাকে তেতো বিমর্ষ করে দিচ্ছিল। মুখ গুম করে থাকলেন।
উমাশশী বললেন, “কথা বলছ না যে বড়। বোবা হয়ে গেলে?”
সারদা আরও খানিকটা চুপ করে থেকে বললেন, “কী হবে বলে! তুমি আমাকে কুকুর বেড়ালের মতো মনে কর, সেইরকম ব্যবহার কর।”
উমাশশী যেন থ’। গালে হাত দিলেন। “কুকুর বেড়ালের মতন করে আমি তোমায় দেখি। এত বড় কথাটা তুমি বলতে পারলে। বত্রিশ বছর বিয়ে হয়েছে, আমিই বরং তোমার লাথিঝাঁটা খেয়ে দিন কাটাচ্ছি।”
“নেভার। তোমায় লাথি মারার মতন পায়ের জোর আমার নেই।…”
“বোলো না, বোলো না। ও-কথাটি বোলো না। আমায় তো মারছই, আমার বাবাকেও ছাড়ছ না! গুরুজন মানুষ, কবে স্বর্গে গেছেন; তাঁকেও তুমি রেহাই দিলে না। ছেলেমেয়ের কাছে ওইসব কুচ্ছিত কথা লিখেছ। লেখে কেউ? আমায় তুমি যা খুশি বলল, সারা জীবনই শুনছি, তা বলে আমার বাবাকেও গালাগাল দেবে!”
সারদা বুঝলেন বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে বোধহয়। বললেন, “তোমার বাবা আমার ঠিক টার্গেট নয়, তোমাকেই…”।
“জানি। কিন্তু কোন দোষটা আমার হয়েছে, কর্তা?”
সারদা চুপ।
উমাশী বললেন, “সেদিন তোমার দুধে মাছিও পড়েনি, টিকটিকিও পড়েনি। জ্বাল একটু কম হয়েছিল। তা আমার এই হাতির গতর নিয়ে রান্নাঘরে বসে দুধ জ্বাল দিতে আর পারি না। এই তো আমার দোষ!”
“দুধের কথা কেউ বলছে না।”
“তবে কি সন্ধেবেলার কথা বলছ? সন্ধেবেলায় মাথা গরম কে করেছে, আমি না তুমি? কোথায় তোমার দাঁতের পাটি, চশমা—সে কি আমি জানব, না আঁচলে বেঁধে রাখব।”
সারদা গম্ভীর। কথা বলছেন না।
উমাশশী বললেন, “রাগের কারণ থাকবে তো? কথায় কথায় মেজাজ, হম্বিতম্বি, গালমন্দ। কোন খানটায় তোমার ত্রুটি হয়? রং গোপালঠাকুরের মতন করে রাখি।”
সারদা বললেন, “গোপাল না গোবৎস?”
“মানে?”
“সেদিন তোমায় কতবার বললুম,” বলতে গিয়ে থেমে গেলেন সারদা।
“কী বললে?”
সারদার গলায় আর কথা ফোটে না। বার দুই ঢোঁক গিলে বললেন, “সেদিন সকালে তুমি যখন পুজো সেরে এসে কাপড়চোপড় ছাড়ছিলে—মাথাটাথা ঘষেছ চুলটুল এলোমেলো, কপালে চন্দনের টিপ, সেমিজ টেমিজ ইয়ে হয়নি—আমি তোমায় কী বলেছিলাম।”
“কী বলেছিলে? বলার মধ্যে তো দেখলাম, রস রসিকর্তা করে ওই হতকুচ্ছিত তোমার গীতগোবিন্দ গাইছিলে।”
“গাইছিলাম। কিন্তু হতকুচ্ছিত কোন জিনিসটা গেয়েছি?”
“গেয়েছ! আমি যেন কচি খুকি, তোমার ওই সব বাজে বাজে বিগলিত বসনং টসনং আমি বুঝি। যত সব অসভ্যতা।”
“তুমি কিছু বোঝ না।” সারদা রোয়াব করে বললেন যেন।
“বুঝি না। আমার বাবা আমায় মুখ্যু করে তোমার হাতে তুলে দিয়েছিল নাকি? তোমার ওই আধিখ্যেতার নিতম্ব, ঘটকুচ, তালফল সবই বুঝি কর্তা। কার সঙ্গে বত্রিশ বছর ঘর করলাম, তা আর জানি না।”
সারদা বললেন, “বোঝ তো সেদিন কেন বুঝলে না—যখন বললাম, দেহি মুখ-কমল-মধু পানম্…”
“বুঝব না কেন, খুব বুঝেছি। কিন্তু তখন চচ্চড়ে আলোয় ঘরের মধ্যে তোমার মধুপানের বহরটাই বা হয় কেন? ঢংয়ের বয়েস তোমার ফুরোয়নি?
“এক একটা সময়ের এক একরকম মুড। তখন একটা মুড এসেছিল। এখন ও-সব কথা বলা মিনিংলেস।”
উমাশশী কয়েক মুহূর্ত স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর গায়ের আঁচল আরও আলগা করে, জামার বোতাম খুলে খাটে শুয়ে পড়লেন। সারদা বিছানায় বসে।
উমাশশী বললেন, “মেঝে থেকে বালিশটা এনে শুয়ে পড়। বাতিটা নিবিয়ে দিও। কেরাসিনের গন্ধ আমি সইতে পারি না।”
খাটটা ছোট। উমাশশীর ওই শরীরের স্থান কুলিয়ে সারদার দেহটি ধরবে কিনা—বুঝতে পারলেন না সারদা। টেনেটুনে একটু জায়গা হতে পারে।
সারদা বললেন, “তোমার কষ্ট হবে।”
উমাশশী জবাব দিলেন, “আমার কষ্ট তোমায় আর ভাবতে হবে না। এই বত্রিশ বছর অনেক ভেবেছ।” বলে একটু থেমে আবার বললেন, “এই কুড়ি পঁচিশটা দিন ঘরে একলা খাটে শুয়ে থেকেছি আর বুক আমার হু হু করেছে।”
উমাশশীর মুখে ‘হুহু’ শুনে সারদা লাফ মেরে মাটিতে নামলেন এবং অত্যন্ত ত্বরিত গতিতে বাতি নিবিয়ে মাটি থেকে বালিশ তুলে এনে স্ত্রীর পাশে শুয়ে পড়লেন।
স্বামীর দিকে পাশ ফিরেই শুলেন উমাশশী। মুখ থেকে পান আর জরদার গন্ধ আসছিল।
সারদা স্ত্রীর মোটাসোটা হাতটি বুকে টেনে নিয়ে বার কয়েক নিঃশ্বাস ছাড়লেন। ছাড়তে ছাড়তে বললেন, “তুমি শুধু ‘দেহি মুখ-কমল-মধু পানম্’ পর্যন্তই দেখলে উমারানী, তার ক’ লাইন পরেই রয়েছে—‘তুমসি মম ভূষণং তুমসি মম জীবনং তুমসি মম ভব-জলধি-রত্নম। তুমি আমার ভূষণ, তুমিই আমার জীবন…”
উমাশশী রঙ্গ করে বললেন, “থাক থাক, অত ভূষণ-টুসন করো না, তোমার তো বুকে ব্যথা, হাতটা ছাড়, বুকে লাগলে ব্যথা করবে।”
সারদা বললেন, “বুক জুড়িয়ে যাচ্ছে! তোমার হাতটা এখনও কেমন নরম।…কিগো আঙুলের গাঁটটাট ফুলেছে নাকি? এখন তো পূর্ণিমা। বাতে কষ্ট হচ্ছে?”
উমাশশী মাথা নেড়ে বললেন, “বাতের কথা বাদ দাও। ও তো তোমারই দোসর।”
সারদা খুব খুশি হলেন। স্ত্রীর অঙ্গে প্রত্যঙ্গে বাত হয়ে থাকার বাসনাই তো তাঁর ছিল। বললেন, “বোস্টমদের সেই গান জান না? সেই রকম। তোমার গায়ে বাত হয়ে জড়িয়ে থাকাও যে কত শান্তির। আহা!”
উমাশশী এবারে এক অদ্ভুত কাণ্ড করলেন। স্বামীর গালে তবলার বোল তোলার মতন করে একটা চুমু খেতে গেলেন, পারলেন না—এই বয়েসে তা কি সম্ভব! ছপ করে শব্দ হল কেমন, পান আর জরদার ছোপ আর গন্ধ লেগে গেল সারদার গালে।
সারদা চোখ বুজে বললেন, “এটা সেদিনের। আজকের আর একটা দাও। অন্য গালটা ফিরিয়ে দিচ্ছি। লাইক এ কৃশ্চান।”
দুজনে যখন পরম আনন্দে চোখ বুজে আছেন, উমাশশী বললেন, “হ্যাঁগো, তা তুমি তো এখানে বসে বসে চিঠিগুলি লিখতে। খামের ওপর ছাপ পড়ত ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া। কেমন করে পড়ত?”
সারদা বললেন, “সে তোমার ছেলে জানে। আমি তো আলগা স্ট্যাম্প লাগিয়ে দিতাম খামে। তোমার ছেলে চিঠি পেয়ে সেগুলো তুলে পুরনো ধ্যাবড়া ডাক টিকিট লাগিয়ে দিত।”
উমাশশী অবাক। “ওমা, এসব ছেলেমেয়েরা করত। কী সর্বনেশে ছেলেমেয়ে। তাই দেখতাম, ওরা চোর-চোর ভাব করে থাকত। তুমি নেই—তাতেও ওদের মন খারাপ দেখতাম না।”
সারদা বললেন, “এটা ওদের ফাদারের সঙ্গে উইথ অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়েছিল।…আরে, তপুই তো আমায় একেবারে ভোরবেলায় সাইকেলে সুটকেস ঝুলিয়ে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে গেল।”
উমাশশী চুপ। খানিকটা পরে বললেন, “ছিছি, ছিছি, ছেলেমেয়েকেও একেবারে বাপের মতন তৈরি করেছ। বুঝবে ওরা মজা। সবাই তোমার উমা হবে না বুঝলে।” বলেই কি খেয়াল হল উমাশশীর, বললেন, “ছেলেমেয়েদেরও বলেছ নাকি, সেদিন তুমি আমার কাছে কী খেতে চেয়েছিলে?”
সারদা জোরে হেসে ফেললেন। বললেন, “ধ্যুত, আমি কি সত্যিই ছাগল নাকি। ওয়াইফ হাজব্যান্ডের ব্যাপার, ওদের কি বলতে আছে।”
মিলনোৎসব
দেওয়াল ঘড়িতে সাতটা বাজল। শব্দ করেই। উনিশ শো একের ইংলিশ ‘রয়েল’ ওয়াল ক্লক ; এখন রয়েলের গলা প্রায় বুজে এসেছে। কেদারহরি বলেন, ওটা রয়েল নয় ‘বয়েল’। তবু ওটা বাজল। সাতটা বাজতেই জয়গোপাল মিত্তির হাত তুলে বললেন, “আর নয়, গল্পগুজব অনেক হয়েছে, এবার কাজের কথা। হাতে সময় নেই। আজ বারোই কার্তিক। চোদ্দোই পুজো।”
বারিদ ভট্টাচায্যি বললেন, “আজ ভূত চতুর্দশী!”
শম্ভ হালদার বললেন, “প্রেতলোকের চোদ্দোটি প্রেতকে আজ ক্যান্ডেল দান করতে হয়, ভট্টাচায্যিমশাই! কেননি?”
বারিদ কিছু বলার আগেই জয়গোপাল লাঠি ঠুকে বললেন, “স্টপ। বলেছি কাজের কথা ছাড়া এখন আর কিছু হবে না। আটটায় আমরা উঠব।”
প্রিয়গোপাল চড়েচড়ে বসলেন, “তা হলে আর দেরি কেন মিত্তিরদা, শুরু হয়ে যাক। কথায় কথা বাড়ে। আটটার জায়গায় ন’টা হয়ে যাবে দেখবেন!”
জয়গোপাল মাথা নাড়লেন। তা তিনি হতে দেবেন না।
জয়গোপাল সম্পর্কে কয়েকটা কথা এখানে বলতে হয়। তাঁর বয়েস বাহাত্তর ছাড়িয়ে গিয়েছে। শরীরে দশ আনা হাড়, চার আনা মেদ মজ্জা, দু আনা পোশাক-আশাক। মাথাটি পুরোপুরি টাকে ভরা, ঘাড় আর কানের দিকে দু-চার গাছা সাদা ধবধবে চুল। তবে মুখটিতে এখনও ব্যক্তিত্ব রয়েছে। লম্বা নাক, বসা গাল, সরু থুতনি। গায়ের রং ফরসা। চোখের দৃষ্টি সতর্ক। জয়গোপাল একসময় জজ-ম্যাজিস্ট্রেটকেও নাকানিচোবানি খাইয়েছেন, পয়লা নম্বর উকিল ছিলেন এই অঞ্চলের। ব্যক্তিত্ব হল ছাই চাপা আগুন। তাঁর সেই ব্যক্তিত্ব যাবে কোথায়! এখনও আছে।
জয়গোপাল মিত্তিরের আরও অনেক কিছু আছে। যেমন এই তেতলা বাড়িটি। পৈতৃক বাড়ি। তিন ভাই থাকেন। সদ্ভাবে এবং সহর্ষে। নীচের তলায় এই ঘরটি জয়গোপালের বৈঠকখানা। এককালে এখানে বসে মক্কেলদের মামলা শুনতেন। এখন এটিকে তিনি নিজস্ব বৈঠকখানা করে নিয়েছেন। সাজসজ্জা সেই পুরনো আমলের। তবে এরই মধ্যে ফরাস তাকিয়ার সঙ্গে দু-এক জোড়া সোফাসেটিও ঢুকে পড়েছে। জয়গোপাল বসেন আর্মচেয়ারে।
জীবনটাকে এখন মোটামুটি ছকে সাজিয়ে ফেলেছেন জয়গোপাল। সকালে এক ঘন্টা ধোপি মাঠে প্রাতর্ভ্রমণ, বেলায় চা আর পরিজ, সংবাদপত্র পাঠ ; বেশি বেলায় কিঞ্চিৎ নুন মেশানো ঈষদুষ্ণ জলে স্নান, স্বল্প আহার, দুপুরে বিশ্রাম, বিকেলে চা ও একটি ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কিট, রামদাস মালিকে নিয়ে বাগান পরিচর্যা। সন্ধেবেলায়’ পাড়ার বুড়োদের সঙ্গে বৈঠকখানায় বসে গল্প। রাত্রে পারিবারিক আসর। শোবার সময় বিগতা স্ত্রীর ছবিতে একটি স্নেহচুম্বন। অবশেষে নিদ্রা।
জয়গোপাল নিজে যদিও নামকরণ করেননি—তবু তাঁর সভাসদরা এই বৈঠকের নাম দিয়েছেন, ‘সজ্জন মণ্ডল’। এই সভার সদস্য হতে হলে বয়েস কম করেও ষাট হতে হবে, ওপরের দিকে কোনো বয়েস-বাধা নেই। তবে আপাতত বয়োজ্যেষ্ঠ বলতে আছেন জয়গোপাল, আর কেদারহরি। দু জনেই বাহাত্তর। আর এক জন ছিলেন, হরেন ঘটক, সত্তর বাহাত্তর টপকে চুয়াত্তরে আসতেই গত বছর নিউমোনিয়াতে চলে গিয়েছেন।
আপাতত গল্পে আসা যাক।
জয়গোপাল ঘরের চারপাশে তাকিয়ে বললেন, “তোমরা কজন আছ?” প্রিয়গোপাল মাথা গুনে বলল, “ন’জন মিত্তিরদা।”
“ওতেই হবে। সারখেল আর মালপানি আসেনি?”
“আসার কথা। সারখেলের চেম্বার বন্ধ হয় সাতটায়। এসে পড়বে।”
বারিদ বললেন, “গর্জন বন্ধ না হলে আসবে কেমন করে?”
“কিসের গর্জন?”
“ওই প্র্যাকটিস আর কী, মিত্তিরদা! সারখেল ডাক্তার এখনও গর্জনশীল—মানে বোরিং প্র্যাকটিস নিয়ে থাকে তো?”
সভ্যরা হেসে ফেললেন।
কেদারহরি পানের পাতায় কিমামের মতন একটু করে আফিং লাগিয়ে গালে রাখেন। বলেন, কাবলি কিমাম। তাঁর গলা এবং চোখ দুইই ঝিমিয়ে আসে সন্ধে বাড়লেই। কেদারহরি বললেন, “মালপানি! সে কোথায়! তারই তো উদ্যুগ বেশি ছিল!”
শম্ভু হালদার মাথা নাড়লেন। “তার একার কেন হবে, আমাদেরও ছিল। আমরাও বলেছিলাম, এবারের কালী পুজোর গোল্ডেন জুবিলিতে—আমরা বুড়োরাও একটা কিছু করব!…মিত্তিরদা, আজ আমরা বুড়োহাবড়া, কিন্তু আপনি বলুন—চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে যখন জোয়ান ছিলাম—তখন কারা বেল দ্য ক্যাট করত।”
ফণিপ্রসাদ বললেন, “আঃ-হা! মা কালী আবার ক্যাট হল কবে! শম্ভু, তুমি যে কী বলো! কালী হলেন, উজ্জ্বল জ্যোতিষাদগ্ধ স্তেষান্ত পরমাং গতিম।’’
শম্ভু হালদার ভুরু কুঁচকে বললেন, “সংস্কৃত শেখাচ্ছ আমাকে।”
জয়গোপাল আবার লাঠি ঠুকলেন। “আঃ, থামো। বুড়ো হলেই বকবক। যত্ত বাজে অভ্যেস। কাজের কথা হোক।…আমরা কী করব, তাই বলো?”
বারিদ ভট্টাচায্যি বললেন, “সে সব তো মোটামুটি ঠিক করা আছে, মিত্তিরদা। কাল পুজো, বিসর্জন। তরশু প্যান্ডেলে ছেলেছোকরারা আর কালী-কমিটি জলসা করবে। নরশু আমাদের সজ্জন মণ্ডলের অনুষ্ঠান।”
“সব বলা-কওয়া আছে?”
“হ্যাঁ। শরদিন্দু, সেনাপতি, অভয়-কমিটির সবাইকে বলে দিয়েছি। ছেলেগুলোকেও।”
জয়গোপাল খুশি হলেন। বললেন, “কাল সকালে বেড়াতে যাবার সময় আমি শরদিন্দুর সঙ্গে একবার কথা বলে যাব।…এবার পুজোর ব্যবস্থা কেমন? সেদিন চোখে পড়ছিল। কাজ চলছে। ভাল বলেই তো মনে হল।”
শম্ভু হালদার বললেন, “খারাপ কেন হবে, দাদা? ট্রাডিশন বলে একটা কথা আছে। রঘুপুরে কোনওদিন খেলো কুচ্ছিত কালীপুজো হয়েছে? পঞ্চাশ বছর আগে যেভাবে ভাবভক্তি দিয়ে শুরু হয়েছিল সেই ভাবেই আছে। প্রত্যেকটি মরাল কোড মেনে।”
ফণিপ্রসাদ মজা করে বললেন, “রঘুবংশ তো ফেলনা নয়!…তবে সেই পঞ্চাশ বছরের পুরনো পাড়া তো আর নেই। তখন এই পাড়া ছিল ধাপধাড়া, শহরছুট ; বুনো কুল, টোকো আমড়া আর আঝোপে ভরা। রেল লাইনের দিকে মারশি—পেঁকো জমি। হাতে গোনা বাড়ি। তখন আমরা হ্যাফ প্যান্ট পরি, মাঝে মাঝেই লেটার বক্স খুলে যায়…”
সকলেই জোরে হেসে উঠলেন।
হাসি থামলে জয়গোপাল বললেন, “তা ঠিক। তবে তোমাদের চেয়ে আমার দেখাশোনা খানিকটা বেশি হে! আমি সিনিয়ার মোস্ট।”
কেদারহরি আধবোজা চোখে মাথা নেড়ে বললেন, “মিথ্যে বলিস না মিত্তির। আজ ভূতচতুর্দশী, মাথার ওপর মঘা আছে। তুই ভাই আমার চেয়ে বারো দিনের ছোট। …এক আঁতুড়ে জন্মাইনি বলে তুই সিনিয়ার মোস্ট হয়ে যাবি!”
“তোর পাঁজিতে ভুল আছে। ভুল ছক। নতুন ক্যালকুলেশানে পিছিয়ে যাবি।…যাক, বাজে কথা থাক, ফণী কী বলছিল!”
ফণিপ্রসাদ বললেন, “বলছিলাম ট্রাডিশানের কথা। আপনার ইয়াং এজে যেমনটি দেখেছেন, আমরা ছেলেবেলায় যেমন দেখেছি— সব তেমনই আছে। হ্যাঁ, তখন পাড়া ছোট বলে পুজোর চেহারাটা ছিল খানিকটা টিমটিমে ; এখন পাড়া বড়, লোকজন অনেক ; কাজেই ব্রাইটনেস বেড়েছে। তবে মিত্তিরদা, পুরনো কোড ভাঙা হয়নি। চাঁদা যে যেমন দেয়, প্রতিমা সেই আগের মডেলেই, মায়ের হাতে খাঁড়া আছে তবে গলায় মুণ্ডমালা নেই, পায়ের তলায় শিব আছে, মা কিন্তু ঊর্ধবনেত্র। গায়ের অলঙ্কার মাকে ঢেকে রেখেছে। ভেরি বিউটিফুল।”
শম্ভু হালদার বললেন, “ফণী আসল কথাটাই বলল না। আসল কথা হল, পুজো আমাদের ভালই হয় মিত্তিরদা, আপনিও জানেন। যা হয় না, কোনো কালে এখানে হয়নি, তা হল—ওয়াগান ব্রেকার, গুণ্ডা ক্লাস, ট্রান্সপোর্ট বিজনেসের লোক, চাল চিনি সিমেন্টের ইয়েদের কাছ থেকে কোনো সেলামি নেওয়া হয় না।”
জয়গোপাল বললেন, “তা হলে আমাদের জন্যে যে দিনটা ঠিক করা হল— সেদিন আমরা বুড়োরা কী করব! কিছু ভেবেছ?”
বারিদ ভট্টাচায্যি বললেন, “আমি ভেবেছি।”
“কী?”
“প্রথমে উদ্বোধনী সংগীত, পরে খানিকটা গান-বাজনা—বুড়োদের, শ্যামাসঙ্গীত কালীকেত্তন, শেষে সজ্জন মণ্ডলের সভাপতি মিত্তিরদার অভিভাষণ…”
বারিদের কথা শেষ হয়নি তখনও, দরজায় তিন মূর্তিকে দেখা গেল।
সারখেল ডাক্তার একপাশে, অন্যপাশে মালপানি ; মাঝখানে এক ভদ্রলোক। সারখেল ডাক্তার আর মালপানি মাঝের ভদ্রলোকের দু পাশের দুই হাত এমন করে চেপে ধরে আছেন, যেন দুই সৈনিক দু পাশ থেকে কোনো শত্রুপক্ষের গুপ্তচরকে ধরে রাজ্যসভায় পেশ করছে। নাটকীয় ব্যাপারের মতন দেখাচ্ছিল দৃশ্যটি।
ঘরের সবাই হাঁ করে সারখেলদের দিকে তাকিয়ে।
সারখেল ডাক্তারই কথা বললেন প্রথমে জয়গোপাল মিত্তিরের দিকে তাকিয়ে। “দেখুন মিত্তিরদা, কাকে ধরে এনেছি।”
বৈঠকখানার কেউই বুঝতে পারছিলেন না—কাকে ধরে আনা হয়েছে। মাথায় কালো মাদ্রাজি টুপি, গায়ে গলাবন্ধ কোট, পরনে প্যান্ট।
জয়গোপাল বললেন, “কে ও?”
“আমাদের ইউ. জি. ঘোষ। উদয়গোপাল। ইউ. জি.-কে আমরা আন্ডার গ্র্যাজুয়েট ঘোষ বলতাম, মনে পড়ছে না?”
প্রিয়গোপাল যেন লাফিয়ে উঠলেন, “আরে আরে, ইউ. জি. !… এ জুয়েলকে তুমি কোথথেকে পেলে সারখেল?”
মালপানি বললেন, “ধরতে হয়েছে। ইফ দেয়ার ইজ এ উইল দেয়ার ইজ এ ওয়ে…।”
জয়গোপাল ধাতস্থ হয়ে এসেছিলেন। বললেন, “সত্যিই উদয় নাকি?”
উদয়গোপাল হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সকলকে নমস্কার জানালেন। বললেন, “আমি উদয়গোপাল ঘোষ। ইউ. জি.। আমাকে এখানে ইনভাইট করা হয়েছিল। মালপানি লিখেছিল, আমরা কালী পুজোতে গোল্ডেন জুবিলি করছি, তুমি অবশ্যই এসো।আমি এসেছি।”
শম্ভু হালদার বললেন, “সেই যে তুমি পালিয়ে গিয়েছিলে, কত বছর হল যেন, পঁচিশ ত্রিশ বছর—তারপর এই তোমার উদয়!”
ইউ. জি.—মানে উদয়গোপাল বলল, “তিরিশের বেশি, শম্ভুদা। আমি পালিয়ে গিয়েছিলাম সিক্সটি টুয়ে…সঙ্গে ললিতা ছিল। ললিতা এখনও আছে। তাকে আনতে পারলাম না। অনেক কাজ…।”
“তুমি এখন আছ কোথায়?” বারিদ জিজ্ঞেস করলেন।
“সাউথে। পাট্টা ডাকালে…!”
“সেখানে কী কর?”
“আমাদের ক্লিনিক আছে। ন্যাচারাল এলিমেন্ট অ্যান্ড হারবাল মেডিসিন দিয়ে নানা রকম অসুখের চিকিৎসা করা হয়। ললিতা সেখানকার সুপারিনটেনডেন্ট।”
“তুমি?”
“ডাক্তার…। ডাইরেক্টারও।”
“বা বা, বেশ। তা তোমায় খুঁজে বার করল কেমন করে মালপানি?”
“মালপানির এক শালী আমাদের ওদিকের একটা টেকনিক্যাল স্কুলের লাইব্রেরিয়ান। সে একবার অ্যাকসিডেন্টালি আমাদের কাছে এসেছিল। তখনই..!”
“বুঝেছি। ভেরি ওয়েল। তোমায় আমরা ওয়েলকাম করছি—!”
জয়গোপাল বললেন, “না, তা কেমন করে হয়! উদয় এসেছে এ খুবই সুখের খবর। উই আর অল হ্যাপি। কিন্তু আমাদের মধ্যে ওকে জায়গা দেব কেমন করে! ওর বয়েস কত? ষাট না হলে তো এনট্রি পাবে না।”
সারখেল বললেন, “মিত্তিরদা, ইউ. জি. সবে একষট্টি। আমি চেক আপ করে নিয়েছি আগেই। ওর মাথায় কিছু নেই, নি-কেশ। তাই টুপি লাগিয়েছে। দাঁত ফলস— মানে বাঁধানো। বি. পি, তলায় এক শো ওপরে দেড় শো। হার্ট…!”
মালপানি বললেন, “ইউ. জি.-কে গ্রেস দিয়ে পাস করাতে হবে না, দাদা। ও এমনিতেই বেড়া টপকে গিয়েছে।”
জয়গোপাল তিনবার লাঠি ঠুকে বললেন, “উদয়, তুমি আমাদের মণ্ডলিতে প্রবেশাধিকার পেলে! খুশি হলাম।… যাক, আমাদের এখানে কী কথা হচ্ছিল— তোমার জানা দরকার। সারখেল আর মালপানিও শুনুন।… বলো হে তোমরা যা ভেবেছ বলো। আমি একটু আসছি…!”
কেদারহরি বললেন, “তুই কি ওঁ জলং তৎসৎ করতে যাচ্ছিস! তা হলে আমিও যাব!”
“আয়।”
খানিকটা পরে জয়হরিরা— মানে জয়গোপাল আর কেদারহরি ফিরে এসে দেখলেন, উদয় অন্যদের তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে বলছেন, “এই কী একটা মেনু! মানে সজ্জন মণ্ডলের গোল্ডেন জুবিলির অনুষ্ঠানের প্রোগ্রাম! সেই থোড় বড়ি খাড়া! খাড়া বড়ি থোড়! গান, শ্যামাসঙ্গীত, সভাপতির বক্তৃতা! ও কেউ শুনবে না। লোক উঠে যাবে। প্যাণ্ডেল ফাঁকা।”
“তা হলে?” জয়গোপাল বললেন।
“আমি একটা ভেবে এসেছি। আসবার সময় ট্রেনে বসে ভাবছিলাম। লং জার্নি! যদি অভয় দেন, বলি।”
“বলো!”
“একেবারে নতুন ধরনের হবে! ইন্টারেস্টিং! লেগে যাবে।”
“আগে তোমার প্ল্যানটা শুনি।”
উদয়গোপাল একবার সারখেল আর মালপানির দিকে তাকালেন। চোখে চোখে কথা হল। মানে উদয় আগে থেকেই বন্ধুদের মতলবটা শুনিয়ে রেখেছেন। সারখেল চোখ টিপলেন, গো অন…!
উদয় বললেন, “দাদারা, এটা তো এখানকার কালী পুজোর পঞ্চাশ বছর— গোল্ডেন জুবিলি, আপনাদের বয়েসের তো নয়,সে জুবিলি সবাই পেরিয়ে এসেছেন! আজ যাঁদের বয়েস ষাট, পঁয়ষট্টি, সত্তর ছাড়িয়ে গেল— তাঁরা—মানে তাঁদের কাছ থেকে লোকে দু’পাঁচটা মজার কথা, জীবনবাণী, কী বলে গার্হস্থ্য উপদেশ, সহজ সত্যকথা শুনতে চায়। কাজেই আমি একটি ভাবনাচিন্তা করেছি।”
“বলে ফেলো। অকারণ বাকবিস্তার করো না। আটটা সোয়া আটটার মধ্যে মিটিং শেষ করে কচুরিবিলাসে বসতে হবে,” বারিদ বললেন। বলেই নাক টানলেন। এই ঘরের কাছাকাছি এক ঘেরা-বারান্দায় জয়গোপালের নিজস্ব বাবুর্চিখানা। সেখানে, কুকিং বুথে, মিত্তিরমশাইয়ের হুকুমমতন বন্ধুবান্ধবের জন্যে চা ও এটা-ওটা খাবার তৈরি হয়। বলরাম হল কুক। হাত ভাল। মিত্তিরমশাইদের বৃহৎ সংসারের সঙ্গে এই রান্নাঘর বা চা পর্বের কোনো সম্পর্ক নেই।
উদয় বললেন, “কচুরিবিলাসটা কী?”
“নতুন টাটকা কড়াইশুঁটির কচুরি। হিং সমেত।”
উদয় সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বললেন, “বাঃ, বাঃ! দারুণ! তা হলে আমি থাকতে থাকতে একদিন কালিয়াদমনও হয়ে যাক।”
বারিদ বললেন, “সেটা আবার কী হে!”
“তেমন কিছু নয় দাদা, ভাল পাকা মাছের কালিয়া। তাকেই বলি কালিয়াদমন।”
সবাই হেসে উঠল।
শম্ভু হালদার বললেন, “ইউ. জি. তুমি সাউথে থাক বলছ! বাংলাটা এখনও জিব দিয়ে ভালই খসছে তো!”
“আজ্ঞে, আমি অবসর সময়ে বাংলা নভেল লেখার চর্চা করি, আর পুরনো বাংলা বইপত্র যা জোটাতে পেরেছি তাই পড়ি। কথাটা আমার নয়, কেদার বাঁড়জ্যের। বই খুলে দেখতে পারেন।”
জয়গোপাল হাত তুলে বললেন, “স্টপ। তোমরা থামো। ওই দেখো সাড়ে সাতটা বেজে গিয়েছে। সাতটা চল্লিশ। উদয়, তুমি কাজের কথা বলো। সময় নষ্ট কোরো না।”
কচুরিবিলাসের জন্যে সবাই তখন ব্যস্ত। অকারণ বিলম্ব কারও পছন্দ নয়।
উদয় বার দুই গলা পরিষ্কার করে নিয়ে নিজের প্ল্যান বাতলাতে লাগলেন।
যথারীতি আপত্তি উঠল, অসুবিধের কথা তোলা হল, এমন কি সন্দেহ প্রকাশও করা হল উদয়ের অনুষ্ঠানের ভবিষ্যৎ নিয়ে। কিন্তু সারখেল, মালপানি, প্রিয়গোপাল উদয়ের প্রস্তাবকে সরবে সমর্থন করলেন।
জয়গোপাল আর ভোট নিলেন না, তাঁরও পছন্দ হয়েছিল ব্যাপারটা। তিনি বললেন, “তবে তাই হোক। বেশ নতুনই হবে। শম্ভু, তুমি আর সারখেল পাড়ার মধ্যে ব্যাপারটা বলে দাও। ছেলেদেরও জানিয়ে দিও ; মাইকে বলে দেয় যেন আমাদের কথা। তবে ডিটেল না বলে। বুঝলে?”
দুই
কালীপুজো, দেওয়ালি উৎসব, বিসর্জন, ছেলেদের আর কালী-কমিটির জলসা শেষ হয়ে যথা দিনে সজ্জন মণ্ডলের উৎসব বা অনুষ্ঠান শুরু হল।
কার্তিক মাস প্রায় শেষ হতে চলেছে। সামান্য ঠাণ্ডাও পড়ছিল আজকাল। বাজি পটকার চোটে সেই ঠাণ্ডা ভাবটাও আচমকা কমে গিয়েছিল মাঝের ক’দিন। আজ আবার ঈষৎ ঠাণ্ডা দেখা দিয়েছে, কুয়াশাও জমছে চারপাশে, আকাশের কালো পটে তারা বেশ উজ্জ্বল।
রঘুপুরের কালীবাড়ির মাঠে মাঝারি ধরনের প্যান্ডেল। শ চার পাঁচ লোক অনায়াসেই বসতে পারে চেয়ারে বেঞ্চিতে। আলোটালোর ব্যবস্থাও ভাল। সভা মণ্ডপটিতে কোনো জমকালো ব্যাপার নেই। সাধারণভাবে সাজানো। তবে ওই যে পঞ্চাশটি বড় বড় প্রদীপ প্রায় গোল করে জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে, আর আশেপাশে চার পাঁচ জোড়া ছোটবড় হরিনাম-লেখা চাদর পেছন দিকে পতাকার মতন উড়ছে— এটি বেশ দেখাচ্ছিল। কিছু ফুলও অবশ্য আছে।
সভার জায়গাটি আগেই করা ছিল। স্টেজের দু দিকে তিনটি করে চেয়ার। দুটি টেবিল। মানে এপাশে তিন ওপাশে তিন, মোট ছটি চেয়ার, দুটি টেবিল। মাঝমধ্যেখানে সামান্য পেছনে আরও একটি টেবিল ও দুটি চেয়ার। তারও পেছনে প্রায় সিংহাসন মার্কা একটা চেয়ার, সামান্য উঁচুতে, একটি ছোট টেবিল। মাইক-ম্যান চার টেবিলে চারটি মাইক লাগিয়ে দিয়েছে।
সাতটা বাজার আগেই পাড়াপড়শিরা মণ্ডপে জুটতে শুরু করল। কালী-কমিটির ছেলেরা কয়েকটা তুবড়ি জ্বালিয়ে দিল, পটকা ফাটাল, হাউই উড়িয়ে দিল আকাশে। অর্থাৎ সভা শুরু হতে চলেছে, আয় তোরা সবে ছুটিয়া। পাড়ার বুড়োবুড়ি থেকে মধ্যবয়স্ক ভদ্রজন, বউ, বাচ্চা সবাই এসে ভিড় করে ফেলল প্যান্ডেলের তলায়।
এমন সময় মালপানি স্টেজের মধ্যে দাঁড়িয়ে পেটা ঘণ্টায় সাতটা ঘন্টা বাজিয়ে দিলেন।
ইউ জি— মানে উদয়গোপাল একেবারে বাঙালি বয়স্ক ভদ্রলোকের মতন পোশাক আশাক পরে স্টেজের মাঝখানে এসে হাত জোড় করে বললেন, “নমস্কার, নমস্কার। সুধীজন ও ভাইবোনেরা, সবাইকে নমস্কার। আমি উদয়গোপাল ঘোষ। আপনাদেরই লোক। পেটের দায়ে বিভুঁয়ে পড়ে আছি। কিন্তু তবু আমি আজ এসেছি— আপনাদের স্নেহভালবাসার টানে।…আজ এখানে কী অনুষ্ঠান হবে তা সামান্য পরেই দেখতে পাবেন। তার আগে বলি, রঘুপুর কালীপুজোর এটি পঞ্চাশ বছর। সকলেই সেকথা জানেন। আমাদের পুজোর এই গোল্ডেন জুবিলিতে এখানকার, মানে এই পাড়ার বাসিন্দদের মধ্যে যাঁদের বয়েস ষাট পেরিয়ে গিয়েছে, যাঁরা সজ্জন মণ্ডলের সদস্য— তাঁরা একটি অনুষ্ঠান করতে চলেছেন। আমরা এর নাম দিয়েছি ‘বৃদ্ধস্য মিলনোৎসব’।…আমি প্রথমে আমাদের সভাপতির নাম ঘোষণা করছি। প্রস্তাবও করছি। শ্রী জয়গোপাল মিত্র মহাশয়।”
সারখেল ডাক্তার কাছেই ছিলেন, সমর্থন করলেন।
জয়গোপালকে এনে সিংহাসন মার্কা চেয়ারে বসানো হল। জয়গোপাল ধুতি চাদর লাঠি সমেত নিজের জায়গায় বসলেন।
সভা থেকে হাততালির শব্দ হল।
তারপর পাড়ার বিগতজনের জন্যে দু মিনিট শোকজ্ঞাপন।
উদয় ঘোষ বললেন, “এর পর যা তা পরে জানাচ্ছি। তার আগে আমাদের উদ্বোধনী সংগীত হবে। গাইবেন বৃদ্ধরা। আমাদের শম্ভুদা গানটির পরিচালক। তিনিই দলবল নিয়ে গাইবেন। আসুন শম্ভুদা।”
শম্ভু হালদার জনা সাতেককে নিয়ে মঞ্চে উঠলেন। সঙ্গে হারমোনিয়াম ডুগিতবলা, মৃদঙ্গ, খঞ্জনি।
বাজনা গুছোতে খানিকটা সময় গেল। দলে জনা সাতেক থাকলেও গায়ক তিন চার জন। বাকিরা মুখ নাড়বেন, নয়ত মাঝে মাঝে গলা চড়াবেন।
গান শুরু হল।
শম্ভু হালদার গান গাইতে পারতেন এককালে। এখন গলায় জোর পান না।
তিনিই শুরু করলেন, “আমরা সবাই বুড়ো আমাদের এই বুডোর রাজত্বে, বুড়িগুলোর দয়ায় আছি বেঁচে বরতে। আমরা যা খুশি তাই করি, তবু তাঁর খুশিতেই চরি…”
গানের শুরুতেই হাসির দমকা বয়ে গেল মণ্ডপে। গায়করা যে যার খুশি মতন চেঁচাচ্ছেন, শেখানো বানানো গানে ভুলটুল যা পারেন বলে যাচ্ছেন, প্রবলভাবে মৃদঙ্গ আর খঞ্জনি বাজছে। হারমোনিয়ামের রিড আটকে গেছে, তবলা বুঝি ফেঁসে গেল।
হাসির হররা ছুটছে তখন মণ্ডপে। হাততালি। কেউ কেউ সাধু সাধু বলে চেঁচিয়ে উঠল।
উদয় ঘোয চিৎকার করে মাইকে বললেন, “সাধু সাধু নয়, মধু মধু বলুন। এনকোর থেকে বাংলায় মধু বলা যায়। মধু ঋতয়তে বাতাঃ— বাতাসে এখন শুধু মধু। আপনারা আমাদের ধন্য করলেন।”
গান শেষ হল। মণ্ডপে তখনও হাসির ঝড় থামেনি।
কে একটা ছেলে মণ্ডপের বাইরে ডবল তুবড়ি জ্বালিয়ে দিল।
সামান্য চুপচাপ থাকার পর উদয় ঘোষ বললেন, “এবার একটু শান্ত হন। আমাদের পরের অনুষ্ঠান শুরু হবে।” বলে উদয় মালপানির দিকে তাকালেন। মালপানি ঘণ্টা বাজালেন।
উদয় ঘোষ বললেন, “মহাশয় মহাশয়ারা এবার আমরা যা করব, সেটা আপনারা অন্য কোথাও দেখেছেন বলে মনে হয় না। আমরা তিনজন বৃদ্ধকে ওপরে ডাকব। তিনজন বৃদ্ধাকে। দাদা বউদিরা এসে আমাদের কাছে এই মঞ্চে বসবেন। দাদারা রাইট সাইডের চেয়ারে, বউদিরা বাঁ দিকের চেয়ারে। না না, একেবারেই ভাববেন না যে এসব আগে থেকে আমরা ঠিক করে রেখেছি। লটারি করে নাম ঠিক করা হয়েছে দাদা বউদিদের। অবশ্য একটা কথা আগেই বলা উচিত। এই দাদা এবং বউদিরা কেউ কারুর হিজ হিজ হুজ হুজ নয়—মানে কোনো পারিবারিক সম্পর্ক নেই। সেটা থাকলে প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দেওয়ার মতন হত। তাই না।…সারখেল, তুমি দাদাদের বউদিদের নাম ডেকে দাও।”
সারখেল ডাক্তার নীচে থেকেই কাগজে টুকে রাখা নাম ডাকতে লাগলেন। অখিলবন্ধু চক্রবর্তী, মাধবচন্দ্র মজুমদার, গুঞ্জন দত্ত।
“অখিলদা, মাধবদা, গুঞ্জন— আপনারা দয়া করে ওপরে আসুন।”
অখিলরা একে একে ওপরে এলেন। বারিদ আগে থেকেই নোটিশ ঝেড়ে রেখেছিলেন।
এরপর মেয়েরা। সুশীলাবউদি (সুশীলা সরকার), কনকবউদি (কনক মুখখাপাধ্যায়), সতীদি (সতী সেন)।
সুশীলার হাঁটুতে বাত, প্রস্থ অত্যাধিক, বছর খানেক আগে চোখের ছানি কাটিয়েছেন। বয়েস সাতষট্টি আটষট্টি। মাথার কাপড়, পরনে লালপেড়ে সাদা শাড়ি, সিথিতে জ্বলজ্বল করছে সিঁদুর। গায়ে আবার সেন্টও ঢেলেছেন।
সুশীলা কষ্টেসৃষ্টে দু পা এগুতেই দুটো ছেলে ছুটে এসে হাত ধরল। “আসুন, জেঠাইমা।”
উনি মঞ্চে উঠলেন। নিজের চেয়ারে গিয়ে বসতে যাচ্ছিলেন, দেখলেন— বসার জায়গার প্রস্থ কম। তাঁর সাহস হচ্ছিল না।
উদয় বললেন, “বসুন বউদি, এগুলো বাড়ি থেকে আনাননা, ডেকোরেটারের চেয়ার নয়।”
সুশীলা বসলেন, সাবধানে।
তারপর নাম ডাকা হল কনকবউদির। কনকের বয়েস বাষট্টি তেষট্টি। উনি ব্রাহ্মবাড়ির মেয়ে ছিলেন একসময়। তারপর হিন্দুবাড়ির বউ এবং গৃহিণী। একরঙা দক্ষিণী শাড়ি পরেছেন। হালকা রং, ঘি রঙের। পাড় মেরুন ধরনের। মাথায় সামান্য কাপড়। কাঁধের কাছে হাড়ের ব্রোচ। হাতে চুড়ি আর ঘড়ি।
কনকবউদিকে ধরতে হল না, নিজেই মঞ্চে উঠে এলেন। বসলেন সুশীলার পাশের চেয়ারে। বসেই একবার আড়চোখে মাধবচন্দ্রকে দেখে নিলেন।
শেষে ডাক পড়ল সতী সেনের। সতী এঁদের মধ্যে কনিষ্ঠা। সবে ষাট।বেশ রোগাটে চেহারা। মাথার সামনের সব চুল পাকা। গাল সরু। সতী সেন চাকরি করতেন কো-অপারেটিভ ব্যাংকে। বেশ কড়া ছিলেন। সাজসজ্জায় ফিটফাট। তিনিই যা হালকা রঙের ছাপা শাড়ি পরেছেন, গায়ে সিল্কের পাতলা স্কার্ফ।
সতীদি বসতেই উদয় ঘোষ বললেন, “এবার আমি আমাদের সকলের মাননীয়া, এবং পপুলার—শোভাদিকে অনুরোধ করব ওপরে আমাদের মধ্যে আসতে। শোভাদি আমাদের এখানকার মেয়ে কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল হয়ে মাত্র চার মাস আগে রিটায়ার করেছেন। তিনি এই পাড়ার জন্যে অনেক কিছু করেছেন, মহিলা সমিতি, গরিব বাচ্চাকাচ্চাদের পড়াবার জন্য ছোট্ট স্কুল, চ্যারিটেবল হোমিও সেন্টার। শোভাদির গুণের শেষ নেই। শোভাদি—মানে শোভনাদি এখানে থাকবেন মহিলাদের পক্ষ থেকে নয়, তিনি থাকবেন আমাদের পক্ষ থেকে। সভার পরিচালনা তিনিই করবেন, আমি তাঁকে শুধু সাহায্য করব। আসুন শোভাদি।”
শোভনা উঠে এলেন সামনে থেকে। চেহারাটি গোল, মাথায় খাটো, গায়ের রং ফরসা, মাথার কোঁকড়ানো চুল কাঁচা পাকায় মেশানো। ঘাড় পর্যন্ত চুল। চোখে চশমা, পরনে গরদ শাড়ি। ছোট পাড়। পায়ে হিল তোলা জুতো।
শোভনা আসতেই উদয় বসার চেয়ারটি তাঁকে এগিয়ে দিয়ে, পাশে সরে দাঁড়ালেন।
শোভনা এসেই প্রথমে সভাপতি জয়গোপাল মিত্রকে হাত জোড় করে নমস্কার করলেন, তারপর মঞ্চের সকলকে এবং শেষে মণ্ডপের দর্শকদের।
শোভনা নিজের চেয়ারে বসলেন।
উদয় ঘোষ গলা পরিষ্কার করে বললে, “প্রথমেই একটা কথা বলে রাখি। আমাদের মঞ্চে মাইকের ব্যবস্থা কম। সব কথা হয়ত সকলের কানে যাবে না ভাল করে, ত্রুটি মার্জনা করে নেবেন।… আজকের এই অনুষ্ঠান— যার আমরা নাম দিয়েছি, ‘বৃদ্ধস্য মিলোনৎসব’— সেখানে একটি নতুন ধরনের খেলা হবে। বলতে পারেন ‘বুড়োদের খেলা’ বা ‘বুড়োবুড়িদের মেলা’।…খেলার নিয়মটা আমি বলে দি। আমাদের মধ্যে যে। তিনজন বউদি দিদি উপস্থিত আছেন— তাঁরা ওই তিন বৃদ্ধজন— মানে আমাদের দাদাদের কয়েকটি করে প্রশ্ন করবেন। প্রশ্নগুলি ব্যক্তিগত হতে পারে, সাধারণও হতে পারে। তবে কোনো প্রশ্নই অভব্য, ইয়ে— মানে ইনডিসেন্ট যেন না হয়। মজার মজার প্রশ্ন হবে, মজা এবং রঙ্গটাই আসল। একটু আধটু খোঁচা নিশ্চয় থাকবে, তবে মন্দ প্র্রশ্ন করবেন না। করলে সেটা কাটান যাবে। বাদ যাবে আর কী। আপনারা মনে রাখবেন, দিস ইজ গেইম, এ গেইম অফ লাইফ অ্যান্ড লাফটার।
“আর আমার বলার কিছু নেই। এবার শোভাদির এজলাসে মামলা তুলে দিলাম। নিন শোভাদি।” বলে উদয় ঘোষ মাইকটা শোভনার দিকে এগিয়ে দিলেন।
ওদিকে তিন বৃদ্ধের মধ্যে অখিলবাবুর গলা শুকিয়ে এসেছে। তিনি বরাবরই ডিসপেপটিক এবং আমাশা আর অম্বলের রোগী। নার্ভাস টেনশানে থাকেন। অথচ রেলওয়ের স্কুলে যখন সিনিয়ার অঙ্ক টিচার ছিলেন— দেদার মার দিয়েছেন ছাত্রদের। জ্যামিতিতে তিনি বাঘ ছিলেন। ছাত্ররা আড়ালে নাম দিয়েছিল, জিয়ো-টাইগার। তাঁর লেখা অঙ্কের বই কলকাতার বইপাড়ায় ছাপা হয়েছে, বিক্রিও হয়েছে দেদার। অখিল তাঁর মাথামোটা ছাত্রদের ঘরে বন্ধ করে বিনি পয়সায় অঙ্কও শেখাতেন এককালে।
সেই অখিল আজ অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেলেন। “উদয় এক গ্লাস জল।”
মালপানি ঘণ্টা বাজাতে যাচ্ছিল, ঘন্টা না বাজিয়ে দুটো ছেলেকে জল দিতে বলল টেবিলে টেবিলে।
ফটাফট ছ’ গ্লাস জল চলে এল কাচের গ্লাসে। টেবিলে সাজিয়ে দেওয়া হচ্ছিল।
সুশীলাবউদির সামনে জল রাখতেই তিনি হাত নেড়ে বললেন, “জল কী হবে, ওই বুড়োদের দে। আমাদের জল লাগবে না। বরং পরে একবার পান-জরদা এনে দিস।”
এবার মালপানির ঘণ্টা বাজল। মানে খেলা শুরু। মণ্ডপ থেকে আওয়াজ উঠল, শুরু হয়ে যাক আরম্ভ করে দিন।
শুরু হল।
শোভনা বললেন, “প্রশ্ন মেয়েরাই করবেন। উত্তর দেবেন পুরুষরা। তাঁরা কোনও সরাসরি প্রশ্ন করতে পারবেন না। প্রশ্ন হবে পাঁচটি থেকে বড় জোর দশটি। তার বেশি নয়। পনেরো মিনিট পর্যন্ত এক একজন সময় পাবেন। মনে থাকবে তো? সুশীলাদি আপনি কী বলেন?”
“আমি আর কী বলব! যেমন তোমাদের ইচ্ছে।”
“তা হলে আপনাকে দিয়েই শুরু করি। আপনি এখানে মহিলাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা। আপনি প্রশ্ন করবেন— অখিলদাদাকে। দাদা, এখানে— মঞ্চে আপনি বয়েসে সবার বড়। আমি শুরু করলাম।”
মাইকের দুই ছোকরা ছুঁচোর মতন ছুটে গিয়ে সুশীলা আর অখিলবাবু— যার যার দিকের টেবিলে মাইক ঠেলে দিয়ে অ্যাডজাস্ট করে দিল।
মণ্ডপ থেকে একটা হালকা আওয়াজ শোনা গেল হাসির।
কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ।
তারপর শোভনা বললেন, “নিন, সুশীলাদি শুরু করুন।”
“দাঁড়াতে পারব না বাপু!’
“না না, বসে বসেই বলুন।”
অখিল জল শেষ করে ফেলেছেন। আর একবার মুখ মুছলেন। মণ্ডপে তাঁর স্ত্রী, ছেলে, ছেলের বউ, মেয়ে— মায় নাতনি বুলবুলি পর্যন্ত আজ। আজ একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। পেটটাও মুচড়ে উঠেছে। সুশীলা বউঠাকরুনকে বিলক্ষণ চেনেন তিনি। কথায় কম যান না। জয় বাবা মহাদেব।
সুশীলার স্বামী মণ্ডপের সামনেই বসে আছেন। ছেলেপুলে বউ নাতিরা বসে আছে। তারা মজা দেখছে।
সুশীলা কথা বলতে গিয়ে যেন আটকে গেলেন। কী বলবেন? মাথায় ছাই কিছুই যে আসছে না।
সকলেই তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে।
শোভনা হেসে বললেন, “বলুন সুশীলাদি, লজ্জা কিসের?”
সুশীলার থমকে যাওয়ার ভাবটা কেটে গেল। তিনি অখিলবাবুর দিকে তাকালেন। দু চারটে পুরনো অপ্রিয় কথা মনে পড়ল। পাশাপাশি বাড়ি না হলেও একবার বাড়ির ময়লা বাইরে ফেলা নিয়ে অখিল-গিন্নি মমতার সঙ্গে তাঁর কথা কাটাকাটি হয়েছিল ; আর-একবার মমতার বাড়ির কাজের লোককে তিনি বেশি টাকা দিয়ে ভাগিয়ে নিয়েছিলেন বলে মমতা তাঁকে আড়ালে ‘ঝি-ভাঙানি’ বলেছিল। আর ওই মাস্টার তো এইট ক্লাসে সুশীলার ছোট ছেলেকে অঙ্কে ফেল করিয়ে ক্লাস-ওঠা বন্ধ করে দিয়েছিল আর কি! এবার একবার নেবেন নাকি অঙ্কের মাস্টারকে! …না, না। এসব ব্যাপার অনেক পুরনো। পাশাপাশি ঘটিবাটি থাকলেও ঠোকাঠুকি হয়। সেসব তুচ্ছ ব্যাপার কবেই তাঁরা ভুলে গেছেন। পড়শি হিসেবে মমতার সঙ্গে তাঁর বেশ সদ্ভাব এখন। তা ছাড়া তাঁর সেই ছোট ছেলে এখন জোয়ান, সে হারামজাদা মাস্টারের মেজো মেয়ের সঙ্গে কচু দেবযানী করল গত কালই। সুশীলা কি কচি খুকি? অসভ্য অভব্যও নয়।
সুশীলা হঠাৎ বললেন, অখিলবাবুর দিকে তাকিয়েই, “কত হল আপনাদের মাস্টারমশাই?”
অখিল ঠিক বুঝতে পারলেন না। বললেন, “ছেষট্টি শেষ হল।”
“আপনার বয়েসের কথা বলছি না, সংসারধর্মের কথা বলছি।”
“ও! তা—তা—বছর চল্লিশ।”
“আমার চেয়ে চার বছর কম।…তা চল্লিশ বছরে কেমন লাগল?”
“কেমন।…ইয়ে, যেমন লাগে।”
“ও কী একটা জবাব হল! বলুন, ভাল না মন্দ?”
অঙ্কের মাস্টার অখিল এবার সাহস পেয়ে গেলেন। বললেন, “দিদি, চৌবাচ্চার অঙ্ক জানেন? একদিক থেকে জল ঢুকছে জলে, ওপরের নল দিয়ে ; নীচের নল দিয়ে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে। কম বেশি। সংসারধর্মটা হল সেই রকম, সুখ আনন্দও জোটে, আবার সেগুলো বেরিয়ে গেলে দুঃখকষ্টও জোটে। এইভাবে চলে!”
“ও তা হলে আপনি বলছেন, বিয়ে-থা করে বউ ছেলেপুলে নিয়ে সংসারধর্ম করাটা চৌবাচ্চার অঙ্ক!”
প্রবল একটা হাসির ঢেউ উঠল মণ্ডপে। হাততালির শব্দ। মধু মধু ধ্বনি। বুড়োবুড়ির দল হেসে এ ওর গায়ে পড়লেন।
সুশীলা এবার একেবারে ফ্রি। কোনও সঙ্কোচ নেই আর। গলা বেশ ভালই উঠছে। বললেন, “তা বেশ দাদা, অঙ্কই হল। এবার বলুন তো— বিয়ের সময় মমতার মুখটি কেমন দেখতে ছিল? হাসিহাসি, না, কান্না কান্না?”
অখিলবাবু ইতস্তত করে বললেন, “অত পুরনো কথা কী মনে থাকে!…তবে একটা কথা মনে আছে দিদি। আমি দেখতে বড় রোগা ছিলুম। বিয়ের সময় আমার দাদাশ্বশুর আমাকে কানে কানে বলেছিলেন, ক্ষীণদেহং মীনসম সরোবরে শোভিত হে, পুচ্ছং উচ্চং তুলি ক্রীড়া করে শালা রে—! মানে, তোমার এই রোগা শরীর ওই পুকুরের জলে শোভা পাচ্ছে, তুমি দাদু শালা লেজ তুলে খেলা করে যাও?”
এবার একেবারে চারপাশ অট্টহাস্যে ভরে উঠল। দারুণ জেঠু, মধু মধু…, অতি মধু।
সুশীলা যেন মার খেয়ে গেলেন। অঙ্কের মাস্টার সংস্কৃত বলে। এ বাবা তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি। সুশীলা নিজেও হেসে ফেলেছিলেন। শাড়ির আঁচলে হাসি মুছে নেবার চেষ্টা করলেন।
হাসি থামলে সুশীলা বললেন, “দাদা, আপনি আর মমতা— কে কতবার ঝগড়া করেছে এই চল্লিশ বছরে?”
“এই তো মুশকিলে ফেললেন দিদি। চল্লিশ বছর মানে, ফরটি ইনটু থ্রি হানড্রেড সিক্সটি ফাইভ।…রাফলি সাড়ে চোদ্দ হাজার দিন। বাপের বাড়ির জন্যে একশো দিন বাদ দিয়েছি। না, আমি বলতে পারব না, দিদি। তবে আপনি ওর দিকে সিক্সটি পার্সেন্ট আমার দিকে ফরটি পার্সেন্ট রাখতে পারেন। দোষ হয়তো আমার।”
“আপনি বরাবর রগচটা।”
“সে আমার ধাত। বাকিটা ছাত্রদের জন্যে।”
“আচ্ছা, এবার বক আর যুধিষ্ঠিরের মতন প্রশ্ন করি?”
“করুন! আপনি কি বক?”
আবার হাসির হররা উঠল।
সুশীলা বললেন, “বক তো ধর্ম।”
“তা ঠিক।”
“জগতে কোন স্বামী সবচেয়ে বেশি সুখী?”
“যে স্বামী স্ত্রীর চরণাশ্রিত।”
আবার হাসি। জোর হট্টরোল।
সুশীলা বললেন, “কোন স্ত্রী বেশি সুখী?”
“যার আঁচলে যত ভারি চাবির গোছা থাকে।”
পুনরায় হট্টরোল।
“গেরস্থ জীবনে কে জেগে ঘুমোয়?”
“স্বামী, মানে পুরুষরা।”
“চতুর কত রকমের হয়?”
“এ কোন মহাভারত দিদি?”
“উদ্ভট মহাভারত। চতুর কত রকমের হয়?”
“বলতে পারব না।”
“জীবনটা কেমন?”
“গায়ের বস্ত্রের মতন। গায়ে বস্ত্র দিলে তা ময়লা হয়। ছেঁড়ে ফাটে। তা বলে কি আমরা বস্ত্র ফেলে দিই দিদি! কেচেকুচে সেলাই করে আবার পরি। এই জীবন সেই রকম। ইট ইজ নট ডার্টি, ইট শুড নট বি ডার্টি। যদিও আমাদের জীবনে— আমরা ডার্টকে ঠেকাতে পারি না।”
জোর হাততালি পড়ল মণ্ডপে। রব উঠল মধু মধু।
মালপানি ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন। মানে সুশীলা-অখিল প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ।
ধন্য ধন্য রব নয়, তবে জোর করতালি ধ্বনি উঠল মণ্ডপ থেকে। কেদারহরি চেয়ারে বসে বসে ঝিমোননা গলায় বললেন, “আহা, কী স্বর্গ। মাস্টার লড়েছে ভাল।”
এবার কনক মুখোপাধ্যায়— মানে কনকবউদি ভার্সেস মাধবচন্দ্র মজুমদার।
শোভনা নাম ঘোষণা করলেন, কনকবউদি আর মাধবচন্দ্রের।
মাইকের ছোকরা দু তরফের টেবিলের মাইক সরিয়ে জায়গা মতন করে দিল।
উদয়গোপাল বললেন, “এবার যাঁরা মুখোমুখি হচ্ছেন তাঁরা দু জনেই এই পাড়ার একেবারে পুরনো বাসিন্দে না হলেও কিছুদিন পরে এসেছেন—তবু পঁচিশ তিরিশ বছর হয়ে গেল। আসুন তাঁদের কথা শুনি।”
শোভনা কনকবউদির দিকে তাকালেন। হাসলেন। “নিন, শুরু করুন।”
মাধবচন্দ্র অখিলবাবুর মতন ডিসপেপটিক রোগী নন। তেষট্টি বছরেও ঘোরাফেরা, সাইকেল স্কুটার চড়া, হাটবাজার— সবই করেন। বাড়ির সারাই-টারাই নিজেই দেখেন শোনেন। কর্মক্ষম মানুষ। খাওয়া-দাওয়ায় রুচি আছে। পানেও। মাধবচন্দ্রের মুখটি গোল, সামান্য ভোঁতা নাক, জ্বলজ্বল করছে চোখ। মাথায় আধ সাদা চুল অল্প হলেও মাঝখানে সিঁথি রেখে ব্যাক্ ব্রাশ করা। গায়ের রংটি কালো।
মাধবচন্দ্র এমনভাবে মাইকের সামনে ঝুঁকে বসলেন, যেন তিনি কিছু কেয়ার করেন না। মিসেস মুখার্জিকে তো নয়ই।
কনকের বাপের বাড়ি ছিল কলকাতায়। ব্রাহ্মসমাজের বাড়ির কাছাকাছি থাকতেন। পড়েছেন বেথুন কলেজে। বাপের বাড়িতে বেশ একটা সমাজ পরিবেশ ছিল। শ্বশুরবাড়িতে অবশ্য পট-পুতুলের হাট। স্বামী দেখতে ভাল, বড় কাজকর্ম করতেন বলে হিন্দুবাড়ির ছেলেকেই পছন্দ হয়ে গিয়েছিল মা বাবার। তা বলতে নেই মুখার্জিমশাই যখন কাজ থেকে অবসর নিলেন— তখন তিনি কাউবয় অ্যান্ড মিল্টন কোম্পানির জোনাল চিফ, ডেপুটি ডিরেক্টর।
কনক একটু গলা পরিষ্কার করে নিয়ে মাধবচন্দ্রের দিকে তাকালেন।
কনক বললেন, “আমি শুরু করছি। আপনি তৈরি?”
মাধব বললেন, “সব সময় তৈরি।”
“আপনি তো পুলিশে কাজ করতেন?”
“সরি ম্যাডাম, আমি পুলিশে কাজ করতাম না। আয়রন ওয়ার্কসের সিকিউরিটি অফিসার ছিলাম। চিফ অফিসার।”
“ওই একই হল। ইউনিফর্ম পরে অফিসে যেতেন দেখতাম…”
“ইউনিফর্ম পরা অফিসিয়াল অর্ডার ছিল। অফিসের পোশাক যদি পরিচয় হয়— তবে তো ডাবের খোল আর নারকোল একই জিনিস।”
মণ্ডপে হালকা হাসি শোনা গেল।
কনক ঘাবড়ালেন না। ঘাবড়াবেন কেন? মাধবের স্কুটার একবার তাঁদের গাড়ির হেড লাইট ভেঙে চুরমার করে দিয়েছিল। গাড়িতে কনক ছিলেন, স্বামীও ছিলেন। মাধবকে দিয়ে তিনি ক্ষমা চাইয়েছিলেন। স্বামী অবশ্য অত্যন্ত অস্বস্তির মধ্যে পড়েছিলেন। অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাসিডেন্ট। তা বলে পাড়ার পরিচিত লোককে কেউ ওভাবে ধমকায়।
কনক ধমকের মেজাজেই বললেন, “আপনি কি নারকোল?”
“বলতে পারেন। আমার মধ্যে জল এবং শাঁস দুইই আছে।”
কনক একটু থমকে গিয়ে তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিলেন। “আপনি—আপনি মিসেস মজুমদারকে টর্চার করেন।”
“শুনুন কনকদেবী, আমি খাস মতি মজুমদারের নাতির ছেলে। কলকাতার বনেদি বংশ। আমাদের বাড়িতে কেউ মিসেস নয়, সকলেই শ্ৰীমতী। আমার শ্রীমতী মানে স্ত্রীকে আমি টর্চার করি, আপনি দেখেছেন?’
“হ্যাঁ, দেখেছি।”
“বলুন?”
“দুটো বাঘা কুকুর, বারো চোদ্দটা বেড়াল, একটা কাকাতুয়া— সব তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন। তার সঙ্গে আবার যিশু-বিশু। যমজ। অবশ্য যিশুরা ভেরি ব্রাইট। তবে প্রচণ্ড দুরন্ত। একে আপনি কী বলবেন!”
মাধবচন্দ্রের স্ত্রী অতসী মণ্ডপে বসে বসে হাসছিলেন। যিশু-বিশু দুই ভাই শিস দিয়ে উঠল। দু জনেই সবে পায়ে দাঁড়িয়েছে, একজন ইনজিনিয়ারিং পাস করেছে সবে, অন্যজন সি এ চালাচ্ছে।
মাধব বললেন, “দেখুন কনকদি, কিংবা লেডিদি, আমি জানি কাজ করলে শরীর ভাল থাকে। কুকুর স্বর্গের জীব। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে একমাত্র কুকুরই ওই হাইটে পৌঁছতে পেরেছিল। আমার স্ত্রীকে ওই আলটিমেট জায়গায় গাইড করে নিয়ে যাবার জন্যে এক জোড়া হেল্পার দিয়েছি। অন্যায় করেছি?”
হো হো হাসি উঠল মণ্ডপ থেকে। জোর হাততালি। মধু মধু রব। কে যেন দুটো পটকা ফাটিয়ে দিল।
মাধব হাত তুলে নিরস্ত্র হতে বললেন মণ্ডপের শ্রোতাদের। তারপর কনকের দিকে তাকিয়ে বললেন, “আপনি বেড়ালের কথা বললেন। ওগুলো হল মাতৃহারা সন্তান। নানা জায়গা থেকে জুটিয়ে আনা। নালা, নর্দমা, ডাস্টবিন, রেললাইন, রাস্তা, ধোপি বস্তি থেকে। ওরা একসঙ্গে লালিত পালিত হচ্ছে মানে ওই যাকে বলে— ওদের মধ্যে একটা ইউনিটি ডেভলাপ করার চেষ্টা হচ্ছে এ-দেশীয় প্রথায়।…আর কাকাতুয়াটা আমি শ্বশুরবাড়ি থেকে যৌতুক হিসেবে পেয়েছি। ওর বয়েস ছাপান্ন। আমায় ‘জামাইবাবু’ বলে ডাকে, বিশ্বাস করুন।”
এবার যেন মণ্ডপ হাসির তোড়ে ভেঙে পড়ল। কী প্রচণ্ড হাস্যরোল। সেই সঙ্গে হাততালি।
মাধব বললেন, “তবে কনকদি, আমি নিশ্চয় কনফেস করব, আমার বেশি বয়েসের দুই ছেলে একেবারে সাউন্ড অ্যান্ড ফিউরি।”
আবার হাসি। যিশু-বিশু জোরে চেঁচিয়ে উঠল, “বাপি, বহুত মাজা আয়া। থ্যাংক ইউ।”
কনক একেবারে বিপর্যস্ত। ওই বুড়োটা—এমন বাক্যবাগীশ জানা ছিল না। তাঁকে একেবারে অপদস্থ করে দিল।
কনক একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, “মজুমদারবাবু, আপনি তো নিজেকে খুব রসিক প্রমাণ করলেন। এবার কটা কথা বলি?”
“বলুন?”
“অতসীদি— মানে আপনার স্ত্রী, মাথায় আপনার চেয়ে এক ইঞ্চি মতন লম্বা কেন?”
“জেনেশুনেই সেটা হয়েছে দিদি। আমি রমণীজাতিকে শ্রদ্ধা করি। সেই জন্যে একটু বাড়তে দিয়েছি।”
হাসি আর থামছিল না।
“অতসীদিকে একবার কাঁকড়া বিছে কামড়েছিল। জ্বালায় যন্ত্রণায় মরে যাচ্ছিলেন। আপনি তখন তাস খেলায় মত্ত ছিলেন। কিস্যু করেননি।”
“হ্যাঁ তা ঠিকই। তবে আমি স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলাম, ভাবছ কেন! আমার মতন বৃশ্চিক নিয়ে তোমার জীবন কাটছে, ওই বেটা পুঁটি কাঁকড়া তোমার কী করবে!”
এবারে হাসির তোড়ে মণ্ডপের চেয়ারগুলো হেলে গেল
কনক রণে ভঙ্গ দিলেন। বললেন, “না, আপনাকে নিয়ে পারা যায় না। ভীষণ অসভ্য আপনি।”
মাধব বিজয়ী হয়েও হাত জোড় করে হাসতে হাসতে কনককে বললেন, “কনকদি, কিছু মনে করবেন না। এ হল মজার খেলা। অপরাধ করে থাকলে মাফ চাইছি।”
“যান! আর ন্যাকামি করবেন না— এই বয়েসে।”
মণ্ডপ থেকে মধু মধু ধ্বনি উঠল। হাততালি। আবার যেন কে দুটো তুবড়ি জ্বালিয়ে দিল।
ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন মালপানি।
শোভনা, উদয়—সবাই তখনও হাসছিলেন।
বাকি থাকলেন সতী সেন আর গুঞ্জন দত্ত।
তাঁদের পালা শুরু হল এবার। শোভনা নাম ডাকলেন। মাইকের ছোকরা মাইক সাজিয়ে দিল।
সতী সেনকে বয়েসের তুলনায় যেন আরও বয়স্কা দেখায়। স্বভাবে সামান্য গম্ভীর, কিঞ্চিৎ উগ্র। চাকরি জীবনে পুরুষদের মাথায় চড়তে দেননি অফিসে। বাড়িতেও তিনি স্বামীর মাথার ওপর। ওঁদের কোনও সন্তানাদি নেই।
গুঞ্জন কোলিয়ারিতে চাকরি করতেন। অ্যাকাউন্টস অফিসার। সবে রিটায়ার করেছেন। এই অঞ্চলের ছেলে। তবে এই পাড়ার বাড়ি তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি। বাবা করেছিলেন পরে।
সতী সেনও এদিককার মেয়ে। তাঁর বাড়ি মাত্র বছর দশেকের। উনি খানিকটা বয়েসে বিয়ে করেছেন। স্বামী ব্যবসা করেন।
সতী গুঞ্জনের দিকে অনেকক্ষণ থেকেই আড়চোখে লক্ষ করছিলেন। পাতিহাঁসের মতন চেহারা হয়েছে গুঞ্জনের এখন। তিনি আর গুঞ্জন আজই শুধু এক পাড়ারই বাসিন্দে নয় এককালে তাঁরা এই শহরের এখানকারই পাশাপাশি দু মহল্লায় থাকতেন দুজনে। মহল্লা আলাদা হলেও চেনাচিনি ছিল। পরিচয়ও ছিল ভাল। তারপর সতী যখন বাইরে পড়তে গেলেন, মেয়ে হোস্টেলে থাকতেন— তখন কলকাতার রাস্তায় গুঞ্জনকে দেখতে পাওয়া যেত। গুঞ্জনও পড়তে এসেছেন। দুজনে প্রায় সমবয়স্ক।
সে-সময় গুঞ্জন মাঝে মাঝে সতীর হোস্টেলে দেখা করতে আসতেন। দুজনে ফুটপাথে পায়চারি করেছেন, চা খেয়েছেন নিরিবিলি রেস্টুরেন্টে মুখোমুখি বসে।
গুঞ্জন দু-চারটে চিঠিও লিখেছিলেন হোস্টেলের ঠিকানায়। সতী জবাবও দিয়েছিলেন। মামুলি চিঠি, তবু তার মধ্যে অল্পস্বল্প ভাবোচ্ছ্বাস থাকত। চিঠির তলায় গুঞ্জন লিখতেন, ‘ইতি তোমার গুনুদা।’ সতী লিখতেন, ‘ইতি স’।
দিনগুলো পালটে গেল। সতীকে ফিরে আসতে হল, পরীক্ষা দিয়ে চাকরি নিতে হল। আর গুঞ্জন পড়া শেষ করে বাপের চেষ্টায় গোকুলপুর কোলিয়ারিতে চাকরি পেল। অর্থাৎ যেটুকু উচ্ছ্বাস ফেনিয়ে উঠেছিল— তা মিলিয়ে গেল। এসব অনেক পুরনো কথা।
সতী চুপ করে আছেন দেখে শোভা বললেন, “সতীদি আপনি শুরু করুন।”
গুঞ্জন চুপ করে বসে। তাঁর চেয়ারের বসার জায়গায় ছারপোকা আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। উসখুস করছিলেন। এমনিতেই গুঞ্জনকে একটু ব্যস্ত দেখায়।
সতী সেন প্রায় না তাকিয়েই বললেন, “আমরা তো এখানকারই লোক, এক সময় শহরের লাহাপাড়ার দিকে থাকতাম। এই জায়গাটা তখন নতুন, গড়ে উঠছে সবে। সেই চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে থেকেই গুনুদাকে আমি চিনি। তারপর কত জল গড়াল, পাড়া বদলাল, গুনুদা কোলিয়ারিতে, আমি এখানে অফিসে। আবার একদিন এই পাড়ায় দুজনেই থাকতে এলাম। গুনুদাদের বাড়ি পুরনো হয়ে গেল। ওর বাবা করেছিলেন। আমারটা ছোট কুঁড়ে। এই তো সবে হল। ..আমি আর কী জিজ্ঞেস করব গুনুদাকে! চেনা-জানা মানুষকে কী আর জিজ্ঞেস করা যায়?”
গুঞ্জন বার কয়েক চোখ পিটপিট করলেন। চোখ দুটি গোল। ছোট। ভুরুতে কয়েকটা পাকা চুল।
শোভনা হেসে বললেন, “এখানে এই পাড়ার লোকরা সবাই তো চেনাশোনা সতীদি। তবু, আপনি কিছু প্রশ্ন করুন। নয়ত ঠিক মানাবে না আজকের এই ব্যাপারটার সঙ্গে।…করুন না, যা মনে আসে তেমন প্রশ্ন! ভালই লাগবে শুনতে।”।
সতী এবার গুঞ্জনের দিকে তাকালেন। কাশলেন মুখ চাপা দিয়ে। তারপর বললেন, “করি তা হলে?…আচ্ছা বেশ, আমার প্রথম প্রশ্ন হল, গুনুদা আগে— সেই লাহা গলিতে থাকার সময় আমাদের দু-তিনজনকে নিয়ে ঘর অন্ধকার করে প্ল্যানচেট করতে বসত। আমার হাতে পেনসিল গুঁজে দিত। ভূতটুত আসত কিনা জানি না, ভয় হত, গা ছমছম করত, কাঁটা দিত। সেই অভ্যেসটা কি আছে?”
গুঞ্জন বুঝতে পারলেন। সেই কিশোর বয়েসে গায়ে গা লাগলে কাঁটা লাগবেই। লাগারই কথা। সতী বেশ খোঁচাটা মারল।
গুঞ্জন বললেন, “না, না। ওসব আর করি না।” বলে ঢোঁক গিললেন।
“কেন? ভূত নেই, না, আর আসে না?”
“সে তখন ছেলেমানুষি করতাম। ও-রকম অনেকেই করে। বড় বড় লোকরাও করেছেন। ফেমাস লোকরা। শখ! ওসব বোগাস!”
“কোনটা বোগাস! ভূত, না, ভূতের হিজিবিজি?”
“ভূত-ভূত করছ কেন! আত্মা! স্পিরিট। আমি ওসবে আর বিশ্বাস করি না।” বলে গুঞ্জন একবার মণ্ডপের দিকে তাকালেন। গিন্নি, দুই মেয়ে, নতুন জামাই বড় মেয়ের, বসে আছে। সতী অন্ধকার ঘরে প্ল্যানচেটের কথাটা না তুললেই পারত!
সতী মুখ টিপে হাসলেন। বললেন, “আমার কাছে ওরকম— ওই ধরনের হিজিবিজি দু একটা আছে!”
গুঞ্জন প্রায় চমকে উঠলেন! ও ধরনের হিজিবিজি মানে! সতী কি অন্য কিছু মনে করিয়ে দিল! উনি একটু ঘাবড়ে গেলেন। “বাজে কথা! কবেকার হিজিবিজি— মিনিংলেস, কেউ রাখে নাকি! তুমি পাগল!”
সতী ঠোঁট কামড়ে হাসলেন। গুনুদাকে বেশ ঘাবড়ে দেওয়া গিয়েছে। মজা লাগল। “আমি পাগল! একদিন তা হলে ঘেঁটেঘুঁটে বার করতে হয় হিজিবিজিগুলো?”
গুঞ্জন আঁতকে উঠলেন। বললেন, “এ আবার কী রে, ভাই! হিজিবিজি কি মানুষের হাতে লেখা। আত্মা এসে ভর করে লেখায়। লেখাগুলো থাকে না, মুছে আসে। শেষে ভ্যানিশ! তুমি পাবে কেমন করে?” মণ্ডপের লোকরা হেসে উঠল।
সতী দমবার পাত্রী নন। হেসে বললেন, “দেখি পাই কিনা! ষাট সত্তর আশি বছর আগের করা সব ছক-কোষ্ঠীর বাসি কাগজ যদি থাকতে পারে, ভূতের লেখা থাকবে না!”
“কী মুশকিল! থাকে না বলেই এখন আমেরিকায় ইউরোপে একরকম টাইপ মেশিন চালু হয়ে গিয়েছে। তার ট্রেড নাম ‘প্ল্যানচেটো’। স্পিরিটরা এসে মেশিন চালিয়ে যায়।”
“কোন স্পিরিট! লোকাল না ফরেন?”
জোর হাসি উঠল মণ্ডপে।
সতী সেন আজ গম্ভীর মেজাজ, রুক্ষ চোখ মোলায়েম করে ফেলেছেন। এ তো তাঁর পুরনো অফিস নয় যে, পুরুষদের জব্দ করার জেদ থাকবে। তা ছাড়া তিনি এখন ভক্তিভরে লীলাপ্রসঙ্গ পড়ছেন, মাঝে মাঝে বসুমতী সংস্করণ পুরনো বিদ্যাপতি গ্রন্থাবলির পাতা উল্টে মনে মনে গানও গেয়ে ফেলেন দু-এক কলি। স্বভাবতই মেজাজে কিঞ্চিৎ আর্দ্রতা এসেছে।…আজকের অনুষ্ঠানও মজার। অকারণে খোঁচাখুঁচি টিপ্পনি কেন?
সতী একটু ভেবে বললেন, “গুনুদা, ভূত থাক। অন্য কথা। তুমি রোজ সকালে দুধ আনতে কৈলাসের খাটালে যাও না?”
“যাই। এক ঢিলে দুই পাটি মারা হয়। মর্নিং ওয়াক হয়ে যায় আর দুধটা খাঁটিও পাই।”
“দুই পাখি কেন? বলো তিন পাখি?”
“মানে!”
সতী চোখ টেরা করে হেসে বললেন, “রসময় মিষ্টান্ন ভাণ্ডারেও তো বেঞ্চির ওপর বসে থাকো।”
“হ্যাঁ। এক পেয়ালা চা খাই বসে বসে। মর্নিং টি!”
“তা খাও। কিন্তু ছোট প্লেটে আলাদা করে কী খাও? রসগোল্লা! তাই না!”
গুঞ্জন এবার বিপদে পড়ে গেলেন। থতমত খেয়ে বললেন, “রোজ খাই না, মাঝে মাঝে খাই। রসময় আগের দিন রাত্তিরে যে টাটকা রসগোলা বানায়— দিশি চিনির— মানে গুড়ের ব্যাপার থাকে, সেটা খেতে খুব ভাল! খেয়েছ? ওটা ভাটপাড়া ব্র্যান্ড।”
নীচে মণ্ডপের সামনে থেকে সারখেল ডাক্তার চেঁচিয়ে উঠলেন। “আরে, দত্তর যে দুশো সত্তর ব্লাড সুগার। ফটাফট সুগার বাড়ছে। মাই গড, রোজ সাত সকালে রসগোল্লা খায়?”
গুঞ্জনের ছোট মেয়ে তার মাকে না ঠেলে বলল, দেখেছ মা!
গুঞ্জন মাথা নাড়তে লাগলেন। “মিথ্যে কথা। দু শো সত্তর আমার বাবার ব্লাড সুগার ছিল। আমার এক শো সত্তর। বাবাকে আমার ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে।…আর রোজ খাই না! বিশ্বাস করুন!…সতী আমায় নিয়ে মজা করছে!’
সভায় হাস্যরোল উঠল।
সতী হেসে বললেন, “বাঃ, মজা করব কেন! যা দেখেছি তাই বলছি।”
“ইমপসিবল! কেমন করে দেখবে তুমি? দূরবিন কষে!”
“রসময়ের কাছে শুনেছি গুনুদা! তুমি রসগোল্লা খাও, গরম জিলিপি খাও, গজাও খাও…! মিথ্যে কথা বলছ কেন! বুড়ো বয়েসেও মিথ্যে কথা বলবে! খনা বলেছে, যদি ঠকাও পঞ্চাশে, বাঁধা পড়বে নাগপাশে…”
“ড্যাম ইওর খনা!” গুঞ্জন বললেন।
“ওমা, ওকি কথা! বউদির নাম যে খনা!”
প্রবল হাসি শোনা গেল মণ্ডপে। গুঞ্জনের খেয়াল ছিল না তাঁর গিন্নির নাম খনা। বড় অপ্রস্তুতে পড়লেন গুঞ্জন।
সতী এবার বললেন, “আচ্ছা, আর বেশি তোমায় জ্বালাব না। এবার সোজা সোজা প্রশ্ন। …সেই পদ্যটা তোমার মনে আছে? বিয়ের সময় যেটা ছাপা হয়েছিল তোমার?”
“না। বিয়ের পদ্য কে মনে রাখে! বড়দি লিখেছিল। বিয়ের পদ্য আর বিয়ের ছাতা কেউ রাখতে পারে কোনোদিন!”
“বড়দির নাম করে নিজে তুমি লিখলে, আমার মামার প্রেসে ছাপালে ; অলি গুঞ্জন, হৃদি মহুন— কত কী লিখলে আর এখন সব ভুলে গেলে!”
“আমার মনে নেই। শুধু মাথার ওপর প্রজাপতিটা মনে আছে। শুঁয়োপোকার মতন দেখাচ্ছিল সেটা। যেমন ছাপা, তেমন প্রজাপতি।”
“তা হলে বলছ, প্রজাপতির বদলে শুঁয়োপোকা নিয়ে জীবনটা শুরু হয়েছিল?”
জোর হাসি উঠল মণ্ডপে, হাততালি পড়ল।
সতী বললেন, “শুঁয়োপোকাই প্রজাপতি হয় গুনুদা। যাক আর মাত্র দুটো প্রশ্ন!” “বলো?”
“বউদির সঙ্গে তোমার কত বছর ঘরসংসার হল?”
“বত্রিশ।”
“কেমন মনে হয় এখন—?”
গুঞ্জন একটু ভেবে রসিকতার গলায় বললেন, “ভেরি ইনটারেস্টিং, এ যেন ভাই, বত্রিশটি দন্ত উৎপাটনের কেরামতি দেখা…!”
হো হো হাসাহাসি। হাততালি। মণ্ডপ অট্টরোলে ভরে উঠল।
সতী সেন এবার বললেন, “আর আমার কোনও কথা নেই।…গুনুদা, কিছু মনে করো না। এক পাড়ায় থাকলেও গল্পগুজব তত বেশি হয় না। তোমার সঙ্গে অনেকদিন পরে একটু ঠাট্টা তামাশা করলাম।…আমাদের বয়েসটা এই ভাবেই এক একদিন হারিয়ে যায়। আজও গেল।”
মালপানি ঘণ্টা বাজিয়ে দিলেন। মানে সতী-গুঞ্জন পর্বও শেষ হল।
শোভনা উদয় ঘোষের দিকে তাকালেন।
উদয় দু হাত তুলে মণ্ডপকে শান্ত হতে বললেন। মণ্ডপ শান্ত হল।
উদয় বললেন, “আমাদের দাদা, বউদি, দিদি, ও ছেলেমেয়েরা। এবার আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হবার মুখে। এখন একটি সমাপ্তি সঙ্গীত গেয়ে শোনাবেন শম্ভুদা ও তাঁর দলবল। আপনারা সামান্য অপেক্ষা করুন।”
শম্ভু হালদার তাঁর দলবল নিয়ে উঠে এলেন মঞ্চে। দলে পুরনোরা প্রায় সবাই, নতুন আরও দু-তিনজন। হারমোনিয়াম মেরামত হয়ে গিয়েছে। ডুগি-তবলা অবশ্য নেই। তার বদলে একটা ঢাক নিয়ে নেমেছেন তারক পালিত। মৃদঙ্গ, খঞ্জনি, কাঁসর-ঘণ্টা সবই রয়েছে।
পাশাপাশি দাঁড়ালেন সবাই। শম্ভু হালদার থিয়েটারি কায়দায় নমস্কার জানিয়ে বললেন, “আমাদের এই গানটি অনেক পুরনো। একালে তেমন শোনা যায় না। আমরা ছেলেবেলায় দু-চারবার শুনেছি। বিখ্যাত এই গানটি আমি এঁদের নিয়ে গাইব। সুর তাল নিয়ে আপনারা ভাববেন না। সুরে কী যায় আসে, প্রাণই তো আসল! আমরা প্রাণমন ভরে গাইব। নেচে নেচে। আপনারাও আমাদের সঙ্গে গাইতে পারেন। তবে নাচতে যাবেন না। চেয়ারে পা লেগে পড়ে গিয়ে বুড়ো বয়েসে হাত-পা-কোমর ভাঙতে পারেন। শুরু করছি। নাও হে হারমোনিয়াম ধরো, মৃদঙ্গ রেডি, নাও হে তারক, বোল দাও।”
বোল উঠল। মৃদঙ্গও বাজল। কাঁসর ঘন্টা। খঞ্জনি।
শম্ভু গলা ছেড়ে গান ধরলেন, “আর যে কদিন আছিস বেঁচে ওরে মন, হরিনাম নিতে ভুলিস না।/ একলা এসেছিস একলা যেতে হবে সঙ্গে তো কেউ যাবে না।”
গানের সঙ্গে সঙ্গে নাচ। একেবারে উর্ধববাহু হয়ে। দশ বারো জনের গলা এবং নাচের চোটে মঞ্চ কাঁপতে লাগল।
মণ্ডপে অট্টরোল। কেদারহরিও নীচে দাঁড়িয়ে নাচতে শুরু করেছেন।
শম্ভুর তখন হুঁশ নেই। গেয়ে চলেছেন, “বাল্যকালে খেলা করে কাটালে/ যৌবনে কামিনী ছাড়লে / বুড়ো হয়েও তবু টাকা টাকা টাকা/ টাকাগুলি তোমার ঘুচলো না…/তাই বলি ওরে মন… যে কটা দিন আছিস বেঁচে হরিনাম নিতে ভুলিস না…।”
গানের তাণ্ডবের মধ্যেই হাততালি, তুবড়ি, পটকা চলতে লাগল। সে-এক মহাদৃশ্য। মৃদঙ্গ ঢোল দুইই ফেঁসে গেল।
গান শেষ হল।
সব যখন প্রায় শান্ত, উদয় ঘোষ বললেন, “এবার আমাদের সজ্জন মণ্ডলের সভাপতি শ্রী জয়গোপাল মিত্র দুটি কথা বলবেন। তারপর সভা শেষ।”
জয়গোপাল একসময় আদালত কাঁপিয়ে দেওয়ানি ফৌজদারি দুই মামলাই লড়েছেন। তাঁর গলা বুজে আসার কোনও কারণ ছিল না। তবু আজ বৃদ্ধের গলা বুজে আসছিল। কোনও রকমে বললেন, “তোমরা আমার কনিষ্ঠ। তুমি করেই বলছি। আজকের দিনটি আমার জীবনে হয়ত আর ফিরে আসবে না। তোমাদের সকলকে আমার আশীর্বাদ আর শুভেচ্ছা জানাই। তোমাদের যেন মঙ্গল হয়।…একটা কথা বলি। উদয় না থাকলে, এমন একটা অনুষ্ঠান হত না। তাকে বাহবা দিতে হবে।…আমার শেষ কথা হল, অখিলমাস্টার যা বলল— প্রায় তাই। একই। দেখো ভাই, জীবন হল সত্যিই এক বস্ত্রের মতন। আমাদের পরনে রয়েছে। এখানে ধুলোময়লা লাগবে, নোংরা হবে, তা বলে জীবন তো ফেলে দেবার নয়! যা মন্দ, যা ময়লা, তা যতটা পারা যায় সাফসুফ করে নিয়ে বাঁচতে হবে। তোমরা সেই ভাবেই বাঁচো, ঈশ্বরের চরণে আমার তাই প্রার্থনা।” বলতে বলতে থামলেন জয়গোপাল। চোখে পড়ল, মঞ্চের পঞ্চাশটি প্রদীপের অনেকগুলিই নিবে গিয়েছে। বাকিগুলোও প্রায় নিবে এল।
জয়গোপাল একটু যেন হাসলেন নিজের মনে।
সভা ভঙ্গ হল। বাইরে তখন শেষ কার্তিকের হিম পড়ছে।
র্যাটকিলার
ক্যানটিন থেকে ফিরে এসে মুরারি দেখল, তার টেবিলের সামনে কেদার বসে আছে। কলকাতায় শীত নেই, শীতের ধুলোটুকুই পড়ে আছে। কেদারের গায়ে তবু করকরে জহরকোট, গলায় মাফলার, কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ। কেদার বেশ অধৈর্য হয়ে অপেক্ষা করছিল। তার চোখ মুখ ময়লা, মাথার চুল উস্কোখুস্কো, রুক্ষ।
মুরারি বলল, “কিরে? তুই?”
কেদার বিরক্ত হয়ে বলল, “কোথায় গিয়েছিলি? কখন থেকে বসে আছি।”
চেয়ার টেনে বসতে বসতে মুরারি বলল, “ক্যানটিনে।”
কেদার কেমন আক্ষেপের মুখ করে বলল, “তোদের রাইটার্সে গভর্নমেন্ট যে কত বেকার-ভাতা দেয়!” বলে মুরারির আশপাশের টেবিলের দিকে তাকাল।
বেকার-ভাতা কথাটায় মুরারি হেসে ফেলল। “চা খাবি?”
“না না, এখন চা-ফা নয়। নে নে ওঠ্…অনেক লেট হয়ে গেল।”
মুরারি ইচ্ছে করেই টেবিলের ওপর রাখা কাগজপত্র টানতে লাগল, যেন তার অনেক কাজ, এখন আর ওঠার সময় নেই। সিগারেটের প্যাকেটটা কেদারের দিকে এগিয়ে দিল, অর্থাৎ কেদার বসে বসে সিগারেট খেতে পারে কিন্তু মুরারি এখন উঠতে পারবে না।
কেদার মুরারির ভাবভঙ্গি দেখে আরও অধৈর্য হয়ে বলল, “কী রে, ওঠ।”
“এখন কী করে উঠি, অনেক কাজ,” মুরারি নিরীহের মতন মুখ করে জবাব দিল।
“যা যা, কাজফাজ রেখে দে, তোদের রাইটার্সে আবার কাজ, নে নে উঠে পড় ; তিনটে বাজতে চলল, গিয়ে হয়ত দেখব, ও কেটে পড়েছে।”
মুরারি বেশ আরাম করে একমুখ ধোঁয়া টেনে নিয়ে তারপর আস্তে আস্তে নাক মুখ দিয়ে ধোঁয়া বার করতে করতে বলল, “তোমার ও তুমি বোঝ, আমার কী?”
কেদার দু মুহূর্ত বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, “যাঃ, এ রকম করিস না। আমি শালা আসানসোল থেকে কত ঝামেলা করে আসছি, কী রকম হেলপ্লেস্। মাইন্ডের কী অবস্থা, আর তুই মাইরি আমায় স্ট্রেট্ কাটিয়ে দিচ্ছিস।”
মুরারি হেসে ফেলল। কেদার কেন এসেছে, তার এত ব্যস্ততা কিসের, ওর মাইন্ডের অবস্থাটাই-বা কেমন—কিছুই মুরারির অজানা নয়। তবু কেদারকে আরও একটু জব্দ করার জন্যে মুরারি বলল, “দেখো যাদু, তুমি করবে প্রেম; আর আমি গিয়ে তোমার ইয়েকে ডেকে দেব—তা হয় না। ইট্ ইজ্ ইওর বিজনেস… !”
কেদার এবার হাত বাড়িয়ে মুরারির কব্জি ধরে ফেলল। করুণ মুখ করে বলল, “এই শেষ বার, দিস ইজ্ দি লাস্ট্ টাইম ; মাইরি, আমি প্রমিস করছি, আর তোকে বলব না, আই উইল্ অ্যারেঞ্জ মাই ওউন ফিউন্যারেল।”
মুরারি বেশ উঁচু গলায় হেসে উঠল। তার হাসির শব্দে আশপাশের টেবিল থেকে অন্যরা তাকে লক্ষ্য করতে লাগল। মুরারি কেদারকে বলল, “তোর ফিউন্যারেলই বটে।”
“ঠাট্টা কোরো না ভাই,” কেদার বলল, “আমার এখন সেই অবস্থা।”
মুরারিকে উঠতে হল। কেদারও উঠে দাঁড়াল।
চেয়ার ছেড়ে যাবার সময় মুরারি পাশের সহকর্মীকে বলল, “প্রণব আমি একটু আসছি ; মিনিট কুড়ি।”
ঘর থেকে বেরিয়ে প্যাসেজ দিয়ে আসতে আসতে কেদার বলল, “মানসীদের সেক্শন ইনচার্জটা মহা হারামি ; ও বেটা সেক্শনের মেয়েদের নাড়িনক্ষত্রের খবর রাখে, শালা আমায় দেখেছে দু-চার বার, মানসীদের পাড়ার কাছাকাছিই থাকে, বুঝলি না। মানসী স্পটেড হতে চায় না, ভয় পায়। না হলে আমি নিজে গিয়েই স্ট্রেট্ ডাকতে পারতাম।”
মুরারি হাসিমুখে জবাব দিল, “তোমার মানসী ভাই তুমিই জানো। তবে ওদের বড়বাবু আমাকেই না দাগী করে দেয়।”
‘য়াঃ যাঃ, তোকে কী করবে? তোর ক্যারেকটারই আলাদা। তুই হলি মিস্টার ক্যারেকটার। জাস্ট লাইক মিস্টার ইউনিভার্স। এ সব ব্যাপারে পার্টি দেখলেই চেনা যায়। তুই সে-রকম পার্টি নয়, নট্ ইন্ দিস কেস।”
সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় আরও কটা কথা হল। তারপর রাস্তা। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কেদার তার মনের উচাটন অবস্থাটাকে বোঝাতে লাগল, আসানসোলে গিয়ে পর্যন্ত তার খাওয়াদাওয়া ঘুম সুখ স্বস্তি সবই গিয়েছে ; নিদারুণ অবস্থা, এক মুহূর্তও থাকতে ইচ্ছে করে না। দারুণ অগ্নিবাণে দিন কাটছে।
“চিঠি-ফিটি লিখিস না?” মুরারি জিজ্ঞেস করল।
“কোথায় লিখব? অ্যাড্রেস কী? মানসীদের বাড়ির ঠিকানায় চিঠি লেখা চলে না, সেখানে ওর মনুমার্কা বাপ, তেমনি একখানা ফায়ারিং মা। অফিসের ঠিকানায় চিঠি লিখলে হাওয়া হয়ে যাবে, দু-চারটে পাজি টাইপের ছেলে আছে। বুঝলি মুরারি, মেয়ে দেখলেই কাটা ঘুড়ির মতন লটকে নিতে চায়। বলেছিলুম কোনো বন্ধুর ঠিকানা দিতে, তাও দেবে না, লজ্জা করে, ভয় করে। মেয়েদের মাইরি সব ব্যাপারে লজ্জা আর ভয়। মেজাজ খারাপ করে দেয়।…”
“তা মানসী তো তোকে চিঠি লিখতে পারে!”
“গোটা দুয়েক দিয়েছে। দূর, ওর দ্বারা চিঠি লেখা হবে না। এ সব কলাবিদ্যা ওর জানা নেই। ড্রাই মার্কা চিঠি লেখে, যেন শালা রেল অফিসের বাঁধাগত কয়েক লাইন লিখে ক্লেম রিপোর্ট ফেরত দিচ্ছে। থার্ড ক্লাস।”
লালদিঘি দিয়ে শর্টকাট করে এগিয়ে যাবার সময় কেদার বলল, “আজ আমি একটা ফাইন্যাল করে ফেলব। এই ছুটোছুটি আর ভাল লাগে না। আমি ডিটারমিন্ড হয়ে এসেছি, আজ একটা ডিসিশন চাই, ইয়েস অর নো। তুই ভাই একটু প্রেসার দিবি।”
মুরারি ট্যারা চোখে বন্ধুর দিকে তাকাল, বলল, “তোর মানসী, আমার প্রেসার দেওয়াটা কি উচিত হবে?”
কেদার প্রথমটায় ধরতে পারেনি। পরে বুঝে ফেলল। হেসে উঠে বন্ধুর কাঁধে ধাক্কা দিল, “যাঃ শালা, কী বলিস?”
মানসীর অফিস কাছেই, কয়লাঘাটায়। মুরারিকে কেদারের পাল্লায় পড়ে অনেকবারই আসা-যাওয়া করতে হয়েছে। চেনাশোনাও দু চারজন আছে মুরারির। এখান ওখান দিয়ে পথ করে গলে গিয়ে, হই-হল্লা শুনতে শুনতে কাগজপত্রের গন্ধের মধ্যে দিয়ে দোতলায় চলে এল মুরারি। মানসীদের বসবার ঘরের গায়ে-গায়ে বিরাট করিডোর, মোটামুটি ফাঁকা। কেদার ঘরে ঢুকল না, করিডোরের এক প্রান্তে নিরিবিলি দেখে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে সিগারেট খেতে লাগল। মুরারি ঘরে ঢুকে গেল।
খানিকটা পরে মানসীকে দেখা গেল, তার পিছনে পিছনে মুরারি। কেদার চোখ মুখ ভয়ঙ্কর গম্ভীর করে তাকিয়ে থাকল।
মানসীকে দেখলেই মনে হয়, শান্ত লাজুক ধরনের মেয়ে। রোগাটে চেহারা, গায়ের রঙ ফরসা, ছোটখাট মুখ, মাথাতেও মোটামুটি। সুন্দরী না হলেও সুশ্রী। ঘাড়ে মস্ত বিনুনি দুলছে, শাড়ির রঙটা কমলা, হাতে সরু সরু বালা।
মুরারি মানসীকে কেদারের কাছে পৌঁছে দিয়ে বলল, “তোরা কথা বল, আমি যাই।”
কেদার মাথা নেড়ে বলল, “না না তুই থাক। তোর সঙ্গে দরকার আছে।”
“আবার কি দরকার?”
“আছে, ইম্পর্টেন্ট কথা আছে, তুই একটু ওয়েট কর কোথাও।”
মানসী একবার কেদারের মুখের দিকে তাকাল, তারপর মুরারির দিকে। অগত্যা মুরারি এক মুহূর্ত ভেবে বলল, “আমি তা হলে একজনের খোঁজ নিয়ে আসছি, মিনিট দশ পনেরো দেরি হবে।”
মুরারি চলে যাবার সময় মানসীকে একবার দেখল, কেদারের কাছাকাছি মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। প্রেম তরঙ্গের এও এক রঙ্গ। তার হাসি পাচ্ছিল।
আর-এক বন্ধুর সঙ্গে সামান্য আড্ডা মেরে ফিরে এসে মুরারি দেখল, কেদার আর মানসীর মধ্যে একটা প্রচণ্ডরকম অশান্তি চলছে। কেদার ভীষণভাবে হাত পা ছুঁড়ছে, মাথা নাড়ছে, আর মানসী যেন কিছু একটা বোঝাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করছে।
মুরারি দেখতে পেয়েই মানসী তর তর করে এগিয়ে এল। তার চোখ মুখ বেশ ব্যাকুল, শুকনো, খানিকটা যেন ভীত।
কাছে এসেই মানসী করুণভাবে বলল, “আপনি ওকে একটু বোঝান তো। কেমন পাগলামি করছে!”
মুরারি কেদারের দিকে তাকাল। কেদার উঁচু আলসেয় হেলান দিয়ে বেঁকে নাটকের নায়কের মতন দাঁড়িয়ে আছে।
“হয়েছে কী?” মুরারি জিজ্ঞেস করল।
মানসী বলল, “ওকে জিজ্ঞেস করুন। এমন অবুঝ, যা তা বলছে।”
মুরারি কেদারের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল।
“কিরে, কী হল?”
কেদার গম্ভীর মুখে বলল, “হবার কি আছে। আমার যা বলার ফাইন্যাল বলে দিয়েছি।”
মানসী পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল, বলল, “বলে দিলেই সব হয়ে যায়! আচ্ছা, আপনি বলুন, আমাদের সকলকেই বাপ মা ভাইবোন নিয়ে সংসারে বাস করতে হয়। একটা পাগলামী করে ফেললেই হল।”
কেদার গম্ভীর গলায় বলল, “একজনের কাছে যা পাগলামী মনে হচ্ছে, আমার কাছে সেটা লাইফ অ্যান্ড ডেথ…”
“কিন্তু ঝগড়াটা কোথায়,” মুরারি বলল, “কি নিয়ে ফাটাফাটি?”
কেদার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না, তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিগারেট বের করতে লাগল। পকেট থেকে প্যাকেটটা বের করে চোখ না তুলেই বলল, “আস্ক দি আদার পার্টি?”
মানসী মাথা নেড়ে বলল, “না না, যে বলেছে তাকেই জিজ্ঞেস করুন।”
মুরারি বলল, “কেদার, অফিসের মধ্যে হই-হল্লা করে লাভ নেই, সিন ক্রিয়েট হবে। কী হয়েছে?”
কেদার প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে ঠুকতে লাগল। “আমার কাছ থেকে জানতে চাও?”
“হ্যাঁ।”
“বেশ। আমি ওকে বলেছি, এভাবে চলতে পারে না, বিয়ে করতে হবে, রেজিষ্ট্রি ম্যারেজ ; পনেরো দিন টাইম।”
মানসী মুরারির হাত ধরে ফেলে আর কি! বিহ্বল মুখ করে বলল, “আচ্ছা বলুন এই ভাবে বিয়ে করা যায় নাকি! কথা নেই, বার্তা নেই, বিয়ে।”
“কথা নেই, বার্তা নেই মানে—?” কেদার যেন চার্জ করল মানসীকে, “তুমি আমাকে বিয়ে করবে না বলছ? আগে কোনোদিন তুমি একথা বলেছ? বরং তুমি আমায় এই অ্যাসুরেন্স দিয়েছ যে আমাকেই বিয়ে করবে।”
“কী মুশকিল! কী কথার কেমন মানে! আমি যা বলেছি তার থেকে না করছি না!”
“তা হলে কথা নেই, বার্তা নেই—এসব বাজে কথা বলবে না। কথা ছিল, কথা আছে, এখন আমি বিয়ে করতে বলছি,” কেদার গর্জে উঠল।
মানসী আর কথা বলতে পারল না, মানে—তার মাথায় এমন একটা যুক্তির কোনো জবাব আসছিল না।
মুরারি বন্ধুকে বলল, “কিন্তু তুই দুম করে একটা আলটিমেটাম দিচ্ছিস কেন?”
“দিচ্ছি, কারণ আমি আর পারছি না। এনডিওরেন্সের লিমিট ফুরিয়ে গেছে। আমায় একটা ফাইন্যাল করে নিতেই হবে।”
মানসী বলল, “এভাবে ফাইন্যাল হয়? আপনিই বলুন!”
মুরারি বলল, “কেদার, মাথা গরম করে কোনো ডিসিশন নেওয়া যায় না। স্কুল ফাইন্যালের মতন তুচ্ছ জিনিসই কতবার পেছোয়, আর বিয়ের মতন ভাইটাল ব্যাপারে এগিয়ে যাবার আগে ভাল করে ভেবে দেখা দরকার। মানসীর দিক থেকে নানা প্রবলেম থাকতে পারে।”
“ও প্রবলেম প্রবলেমই থাকবে,” কেদার কোনো আমল না দিয়েই বলল, “আমার বাবা খুব গোঁড়া, মা ভীষণ কড়া ; বামুনের মেয়ে কায়স্থ ছেলেকে বিয়ে করছি শুনলে বাবা কুরুক্ষেত্র করবেন—এসব বাজে ফাদার-মাদার প্রবলেম কোনো দিনই যাবে না। ধ্যুত্, ফ্যামিলি আজকাল কোনো প্রবলেম নাকি? সাহস একটু করতেই হবে, যার সাহস নেই সে কেন এতটা এগিয়ে আসে?”
মানসী আমার মুখের দিকে তাকাল। তার সমস্যাটা কেদার যেভাবে দেখছে, অত হাল্কা করে দেখায় সে রীতিমত ক্ষুন্ন। মানসী বলল, “বাঃ, আমাদের সংসারে আর কোনো ঝঞ্ঝাট নেই? বাবা স্কুলে মাস্টারী করে আর মাঝে মাঝে ছেলে পড়ায়। আমার কোনো বড় ভাই নেই, ভাইবোনেরা ছোট। আমার,চাকরিতে কত উপকার হয় সংসারের!”
“চাকরি ছাড়তে বলা হচ্ছে না—” কেদার জনান্তিকে উক্তি করার মতন করে বলল, বলে তার সিগারেট ধরিয়ে নিল।
মুরারি বন্ধুকে বলল, “ও যদি এখানে চাকরি করে আর তুই আসানসোলে থাকিস তা হলে বিয়ের জন্যে এখনই এই চাপ দিচ্ছিস কেন?”
কেদার নিস্পৃহ মুখ করে বলল, “আরে মেয়েদের আমি চিনি। আউট অফ সাইট্, আউট অফ্ মাইন্ড।”
মুরারি হেসে ফেলল।
মানসী ক্ষুব্ধ হয়ে বলল, “আমি কাউকে আউট্ অফ্ মাইন্ড করিনি!”
“তার প্রমাণ আমার কাছে আছে-” কেদার বলল, “যাক, এখন আন্নেসেসারী কথায় কাজ কি, আমি যা বলার বলে দিয়েছি, অ্যান্ড আই ওয়ান্ট মাই অ্যানসার।”
মানসী চুপ। মুরারিও নির্বাক। কেদার আচ্ছা প্যাঁচ কষেছে তো!
মুরারি মানসীকে সাহস দিয়ে বলল, “আপনি না হয় আরও একটু সময় নিন, ভেবেচিন্তে দেখুন।”
কেদার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁঝিয়ে উঠল, “না, আর সময় নেওয়া চলবে না। আজ, এখনই আমাকে ডিসিশন জানাতে হবে, ইয়েস আর নো।”
মানসীর মুখের রঙ অনেকক্ষণ থেকেই ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল, কেদারের জেদ, গোঁ, গর্জনে তার কেঁদে ফেলার অবস্থা হল। মুরারিরও ভাল লাগছিল না, কেদারটা বড় বাড়াবাড়ি করছে, এরকম গোঁয়ারতুমির কোনো মানে হয় না।
মানসী চুপ করে দাঁড়িয়ে, আর মুখ তুলছে না। হয়ত অভিমান কিংবা দুঃখ সামলে নেবার চেষ্টা করছিল।
মুরারি বলল, “কেদার, তুই বড় বাড়াবাড়ি করছিস। একটু সেনসেবল হবার চেষ্টা কর।”
কেদার বলল, “আমি সেনসেবল, আমায় বলে লাভ নেই। আমি যা ডিসাইড করেছি তার থেকে এক পাও সরব না। কাউকে কোনো জোর করার প্রশ্ন এখানে নেই। ওর যদি আপত্তি থাকে ও আমায় স্পষ্ট বলে দিক, আমি আমার ব্যবস্থা করে নেব।”
মানসী মুখ তুলে বলল, “ব্যবস্থা করে নেবে মানে তুমি বিষ খাবে?”
“খাব।”
মুরারি অবাক হয়ে কেদারের দিকে তাকাল। “বিষ খাবি?”
মানসী ততক্ষণে সত্যি সত্যিই মুরারির হাত ধরে ফেলেছে, মুখ পাংশু। গাঢ়, কান্না-কান্না গলায় বলল, “জানেন, ও তখন থেকে বলছে, আমি বিয়ে করতে রাজি না হলে বিষ খাবে!”
“বিষ, না না, বিষ খাবে কেন?”
“খাবে। ও বলছে খাবে। ওর পকেটে বিষ রয়েছে।”
মুরারির মনে হল, তার মাথাটা হঠাৎ বোঁ করে ঘুরে গেল। কী সর্বনাশ, কেদার আবার বিষটিষও পকেটে করে নিয়ে এসেছে নাকি! ঘাবড়ে গিয়ে মুরারি কেদারকে বলল, “তুই পকেটে করে বিষ নিয়ে এসেছিস?”
কেদার আস্তে আস্তে মাথা দোলাল। “ইয়েস, এনেছি।”
“যাঃ, বাজে কথা!”
মানসী বলল, “না না বাজে কথা নয়, পকেটে আছে, আমায় দেখিয়েছে।”
“কী বিষ?” মুরারি কোনো রকমে বলল।
“কী বিষ যেন, আপনি দেখুন না। আমাকে তখন থেকে শাসাচ্ছে।”
মুরারি কেদারকে কিছু বলবার আগেই কেদার তার প্যান্টের পকেট থেকে ছাপ মারা একটা প্লাস্টিকের ছোট প্যাকেট বের করল। হাতের মুঠোয় প্যাকেটটা বার দুই নাচিয়ে বলল, “এটা দারুণ পয়জেনাস, খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে খেলে দু’ঘণ্টার মধ্যে ফিনিশ।”
“বলিস কি। পটাসিয়াম সায়নয়েড নাকি?”
“না, পটাসিয়াম সায়নয়েডে ডেথটা বোঝাই যায় না। ওটা পিসফুল ডেথ। আমি কত কষ্ট করে মরেছি, এটা দেখাতে চাই।”
“ওটা তা হলে কী?”
“এটা র্যাটকিলার।”
মুরারি অট্টহাস্য হেসে ফেলেছিল আর কি। সামলে নিল। তার গা ঘিন ঘিন করে উঠল। প্রায় শিউরে উঠে সে বলল, “মাই গড, তুই শেষ পর্যন্ত মানুষ হয়ে ইঁদুরের বিষ খাবি? ছি ছি!”
“ইঁদুরের বিষে যন্ত্রণা বেশি, নাড়িভুড়ি জ্বলে পুড়ে যায়, মিনিটে মিনিটে বমি, ভেরি ডেনজারাস। বীভৎস।”
কেদার বোম্বাই ফিল্মের শয়তানদের মতন দাঁড়িয়ে ট্যারা চোখে আমাদের দেখতে লাগল।
মানসীর হঠাৎ কি যেন হয়ে গেল, মুখ নিচু করে নিল, হাতের আঙুলে চোখের পাতা মুছল। কেদারের হৃদয়হীনতার পরিমাপ করছিল বোধ হয়, কিংবা বিষ খাওয়া কেদারের বীভৎস চেহারাটা কল্পনা করে কেঁদে ফেলছিল। মৃদু, অস্পষ্ট গলায় মানসী বলল, “বেশ, এতই যখন অবিশ্বাস, আমি বিয়ে করব। কিন্তু…”
কেদার অপেক্ষা করতে লাগল, মুরারিও।
একটু সামলে নিয়ে মানসী বলল, “কিন্তু—এ কথা আমরা ছাড়া এখন আর কেউ জানবে না।” বলে মানসী মুরারির দিকে তাকাল। “আপনার সামনে ও বলুক বিয়ের কথা কাউকে জানাবে না।”
কেদার বলল, “আমার জানাতে বয়ে গেছে।”
মানসী এবার মুরারির জামার হাত ধরে একটু টানল, টেনে কয়েক পা তফাতে চলে গেল। মুরারিকেও কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াতে হল। মানসী বলল, “আমার বাড়ির কথা আপনি সব জানেন না। কথাটা একবার যদি কেউ জানতে পারে আমার যে কী অবস্থা হবে, কেউ বুঝতে পারছে না। আপনি আপনার বন্ধুকে একটু বুঝিয়ে বলুন, বিয়ে আমি করছি তবে কাকপক্ষীও যেন এখন কথাটা জানতে না পারে। ও এমন কিছু করতে পারবে না যাতে লোক জানাজানি হয়ে যায়। আপনি একটু বলুন। ওর কাছ থেকে কথা নিয়ে নিন।”
ভেবেচিন্তে মুরারি বলল, “চলুন, ওর কাছে যাই, কথাবার্তা হয়ে যাক।”
মুরারি সরে আসছিল, মানসী হঠাৎ বলল, “শুনুন।”
দাঁড়াল মুরারি।
গায়ের আচলটা অকারণে কোমরের কাছে গুঁজতে গুঁজতে মানসী বলল, “আপনি ওকে ওসব খেতে বারণ করবেন। আমি তো বিয়ে করতে রাজিই হয়ে গেলাম। আপনি ওটা ওর কাছ থেকে নিয়ে নেবেন।”
মুরারি ঠোঁট বন্ধ করে হাসল।
কেদারের কাছে এসে দাঁড়াল দুজনে।
মুরারি বলল, “কেদার, তুমি তোমার জবাব পেয়ে গিয়েছ। এখন মানসীর তরফে কয়েকটা শর্ত আছে। সেগুলোর কী হবে?”
“কী শর্ত শুনি?”
“বিয়েটা একেবারে সিক্রেট রাখতে হবে। কেউ জানবে না।”
“আমি আগেই বলেছি, বিয়ের কথা অন্তত আমার মুখ থেকে কেউ জানতে পারবে না। আই প্রমিস।”
“বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরই যে তুমি ওকে জ্বালাতে শুরু করবে, বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে বলবে—তা হবে না। সেরকম করলে ও বিপদে পড়ে যাবে। ব্যাপারটা এখন একেবারেই গোপন থাকবে ; পরে সময় এবং অবস্থা বুঝে যা করার মানসী করবে।”
“সেটা কতদিন?”
মুরারি মানসীর মুখের দিকে তাকাল। জবাবটা মানসীরই দেবার কথা। মানসী অন্যমনস্কভাবে বলল, “এখনই আমি কি করে বলব কতদিন। বছর দেড়-দুই কি তারও বেশি হতে পারে। ওই জন্যেই আমি বলছিলুম এখন থাক।”
কেদার বলল, “আমিও বলেছি, বিয়ে করেই আমি কাউকে লিগ্যালি ক্লেম করছি না। এক দেড় বছর যদি কারও নিজের বাবা-মাকে সামলাতে লাগে আমি তাতে পরোয়া করি না।”
মুরারি দুজনকে এক পলক দেখে নিল। বলল, “পরোয়া না করলেই হল। তুমি পরে কোনো ঝামেলা করতে পারবে না। ওয়ার্ড অফ অনার।”
কেদার মাথা নেড়ে ওয়ার্ড অফ অনার দিল।
মুরারি মানসীর দিকে তাকাল, জানতে চাইল আর কিছু শর্ত থাকবে কি না।
মানসী মৌন থাকল। মানে তার অন্য কোনো শর্ত নেই।
ঝামেলাটা মিটে যাওয়ায় মুরারি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ঘড়ি দেখল, অফিস থেকে পালিয়ে এসেছে ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল। না, আর দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। মুরারি অফিস ফিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। “আমি চলি, বড় দেরি হয়ে গেল।”
কেদার বলল, “দু মিনিট দাঁড়া, আমিও যাব। তুই একটু এগো, আমি আসছি।”
মুরারি মানসীকে বলল, “আমি চলি, সেই কখন অফিস থেকে এসেছি।” বলেই তার মনে পড়ল, মানসীর আর-একটা অনুরোধ রাখা হয়নি। কেদারের দিকে তাকিয়ে মুরারি বলল, “ভাল কথা, তোর র্যাটকিলারের প্যাকেটটা আমায় দিয়ে দে।”
কেদার বলল, “রাস্তায় আমি ফেলে দেব তোর সামনে। আচ্ছা তুই এগো, আমি আসছি।”
মুরারি আড়চোখে একবার মানসীকে দেখে নিয়ে প্যাসেজ দিয়ে হাঁটতে লাগল। কেদার আর মানসী কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কথা বলছে।
নিচে নেমে এসে মুরারি একটা সিগারেট ধরিয়ে দু-চার টান দিতে না দিতেই দেখল কেদার এসে গেছে।
রাস্তায় এসে মুরারি বলল, “বিয়েটা হবে কবে?”
“দেখি, একটা দিন ঠিক করে নিই। কাল সকালে তোর বাড়ি গিয়ে ফাইন্যাল করে নেব। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিস তো তোর জানা আছে, সৌমেনের বিয়ে দিয়েছিলি।”
“সৌমেন কেন, অনেকের দিয়েছি, তোদের মতন পার্টি আজকাল অঢেল।”
কেদার হাসতে লাগল।
“কি রে শালা, খুব আহ্লাদ, না?”
“তা তো একটু হবেই, ভাই।”
“কিন্তু, তুই কি বলে র্যাটকিলারের প্যাকেট পকেটে করে নিয়ে এলি? কী চিজ তুই?”
“আরে, ওটা প্রেসার ট্যাক্টিস। প্রেসার না দিলে মেয়েদের দিয়ে কোনো কাজ করানো যায় না।”
“মানসী যদি অরাজি হত কি করতিস?”
“জানি না। মরে যেতাম। ইন্যদি হয় নিজের ফ্যাকট আমি এভাবে ওকে কলকাতায় রেখে দিতে পারছিলাম না। বুঝছিস না, কোনো বাইন্ডিং নেই, হপ্তায় দু হপ্তায় একবার আসি, দেখা হয়, এতে কি আর ভাল লাগে? তা ছাড়া মেয়েদের ব্যাপার, কবে শালা অন্য খাপে ঢুকে যায়, নজর দেবার তো কম নেই।”
“এতে তোর খারাপ লাগছিল। কিন্তু শালা, বিয়ে করেও যখন দেখবি, বউ আর তোতে কোনো ইয়ে নেই, তখন কেমন লাগবে?”
“সে তখন দেখা যাবে। ফিউচার ইজ ফিউচার।…ওসব কথা যেতে দে, শোন—তোর সঙ্গে আমার অনেক দরকার। রেজিস্ট্রির ব্যাপারে একটা ফাইন্যাল করতে হবে। আজ সন্ধেবেলায় তোর সঙ্গে বসলে হত, কিন্তু মানসীর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে ফেললাম। ছুটির পর অন্নপূর্ণার কাছে দেখা করব। আজ আর হবে না, কাল সকালে তোর বাড়ি যাব। এখন একবার বউবাজারে গিয়ে মামার বাড়িতে একটু ফ্রেশ হয়ে নিই।”
কেদার বউবাজারের ট্রাম ধরল। মুরারি অফিসে ফিরতে ফিরতে নিজের মনেই হাসছিল।
দুই
খুব গোপনেই কেদারের বিয়ে হয়ে গেল। শিয়ালদার দিকে এক ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে সে পর্বটা চুকিয়ে দিল মুরারি। জনা তিনেক সাক্ষী ছাড়া কাউকে আনা হয়নি। সাক্ষীর একজন মুরারি, অন্যজন মুরারির বন্ধু, দিল্লিতে থাকে, কলকাতায় এসেছিল দিদির কাছে। মুরারি তাকে জুটিয়ে এনেছিল, বিয়ের পরের দিনই তার দিল্লি চলে যাবার কথা। তৃতীয়জন মুরারির অফিসের আর এক বন্ধু। বিয়ে হয়ে যাবার পর রেস্টুরেন্টে একটু চা-টা খাওয়া হয়েছিল, তারপর মুরারিরা চলে এল ; কেদার মানসীকে নিয়ে ক্যানিং বেড়াতে চলল।
বিয়ের পর প্রথম প্রথম কেদার কলকাতায় এলে মুরারির অফিস বা বাড়িতে গিয়ে দেখা করত। গল্পটল্প হত। এখন আর কেদার মুরারির অফিসে এসে মানসীর কাছে গিয়ে ডেকে দেবার জন্যে জ্বালাতন করে না। ভেতরে ভেতরে ওদের আগে থেকেই কথাবার্তা ঠিক করা থাকে, সেই মতন দেখা-সাক্ষাৎ হয়।
মুরারি একবার জিজ্ঞেস করেছিল, “মানসীর অফিসে তুই যাস না?”
“না। স্ট্রিক্টলি বারণ করে দিয়েছে।”
“কোথায় যাস তা হলে?”
“সে আছে। কলকাতায় জায়গার অভাব কি?”
“কলকাতায় এলেই দেখা করিস?”
“আলবাৎ। কলকাতায় কি আমি ছোলা ভাজতে আসি? এখন ও আমার বউ না? কত রকম গার্জেনগিরি করে! বেশ লাগে মাইরি, অন্য রকম একটা ফিলিং হয়। তুই এসব বুঝবি না, তোর তো এ লাইন নয়।”
মুরারি হো হো করে হেসে ওঠে। পরে বদমাইশি করে বলে, “তোর বউ এটা তুই বুঝিস কি করে?”
“কেন, বউকে বউ বুঝব না? কি বলছিস তুই?”
“না, মানে, ব্যাপারটা হল—বউ বোঝার একটা আলাদা ব্যাপার আছে, তোদের তো সে রকম করে বোঝার ব্যাপার নেই।”
কেদার হেসে ফেলে। “বলেছিস বেশ, মানসীকে বলব।” বলে চা খেতে খেতে লম্বা করে সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে রহস্যময় হাসি হাসে কেদার, তারপর গানের সুরে বলে, ‘যদি হয় নিজের নারী, তার গড়ন পেটন চিনতে পারি।’
মুরারি হাসতে হাসতে বলল, “খুব সুখেই আছিস তা হলে।”
“ওই আছি।” কেদার আর কিছু বলে না।
কেদারের আসা-যাওয়া ক্রমশই কমতে লাগল। কোনো পাত্তাই আর পাওয়া যেত না। মানসীর সঙ্গে আচমকা অফিসপাড়ায় দেখা হয়ে গেলে মুরারি কেদারের খোঁজ করত।
“র্যাটকিলারের খবর কী?”
মানসী সলজ্জ হাসত। “আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি?”
“না, মাসখানেকেরও বেশি তার মুখ দেখিনি।”
“ওমা, আমায় যে বলল, আপনার বাড়ি যাবে!”
“কবে?”
“এই তো এবার যখন এসেছিল,” মানসী দিন তারিখ ভাঙতে চাইল না।
মুরারি ঠাট্টা করে বলল, “এবার মানে কি সেবার? কেমন আছে র্যাটকিলার?”
“এমনি ভালই। হোটেল মেসের খাবার খেয়ে খেয়ে পেট নিয়ে ভোগে।”
“তাই নাকি! বিয়ের পর পেট একটু ভোগায়।” মুরারি আড়চোখে মানসীর দিকে তাকাল।
মানসীর চোখ মুখ হঠাৎ লজ্জায় লাল হয়ে উঠল।
কথাটা বেফসকা বলে ফেলে মুরারিরই জিব কাটতে ইচ্ছে করছিল। কোনো রকমে সামলে নিয়ে বলল, “কেদার এলে একবার দেখা করতে বলবেন, যদি অবশ্য সময় পায়।”
মানসী মাথা এলিয়ে সায় দিল।
কেদার অবশ্য পরের সপ্তাহে এল। গল্প-গুজব করল। বলল, “ভাই, আমি একেবারে সময় পাই না। শনিবার দিন রাত্রে আসি, রবিবার একটু ঘোরাফেরা করি, আবার সোমবার ভোরের গাড়িতে চাপি। শরীরটাও ভাল যাচ্ছে না।”
“মানসী বলছিল, তোর পেটের গোলমাল হচ্ছে?”
“ইন ফ্যাকট্, সেই রকমই। আসানসোলের জল সহ্য হচ্ছে না।”
“কলকাতার জল নিয়ে যাস্ না?”
কেদার রসিকতাটা বুঝতে পেরে চোখ মটকে হাসল।
খানিকটা বসেই কেদার উঠল। “চলি, একবার দক্ষিণেশ্বর যেতে হবে।”
“দক্ষিণেশ্বর? সে কি রে! তুইও কি রামকেষ্ট করতে যাস?”
“না না, যাব একবার। একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে।”
“মানসী?”
“কোথায় মানসী? তোরা আমার চারপাশে ওই মানসী দেখছিস।”
কেদার চলে গেল। আবার যথারীতি তার খোঁজখবর নেই। গরম পড়েছিল সাঙ্ঘাতিক, সেই গরম কেটে বর্ষা নামল। প্রথম বর্ষাও কেটে যাচ্ছে, মানসীর সঙ্গে এর মধ্যে বার কয়েক দেখাও হয়ে গেল মুরারির। মানসীর শরীর সেরে যাচ্ছে, আগের তুলনায় গায়ে মাংস হয়েছে সামান্য, মুখটা ভরাট হয়ে এসেছে, রঙ আরও উজ্জ্বল মনে হয়। ভালই লাগে মানসীকে দেখতে। মুরারির মনে হল, মানসীর শাড়ি-টাড়িও আগের তুলনায় সরেস হয়েছে। দুজনে অল্প কথাবার্তা হয়। মুরারি রসিকতা করে। মানসী লজ্জা পেয়ে কথা এড়িয়ে যায়। মানসীই বলল, কেদার এখন অ্যাকাউন্টেসি পরীক্ষার জন্যে পড়াশোনা করছে, সপ্তাহে সপ্তাহে আসতে পারছে না।
আবার যখন বর্ষা নামল, প্রবল বর্ষা, তখন একদিন মুরারি দেখল, হ্যারিসন রোডের ওপর দিয়ে আধো অন্ধকারের বৃষ্টির মধ্যে রিকশায় চেপে যুগল মূর্তি চলেছে, কেদার আর মানসী। একজন অন্যজনের মুখে বৃষ্টির জল ছিটিয়ে দিচ্ছে।
ডাকব ডাকব করেও মুরারি ডাকতে পারল না। তার একটু হিংসেই হল, কেদার শালা দিব্যি আছে, মহা ফুর্তিতে।
এর কয়েকদিন পরেই মুরারির মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।
অফিসে নিজের টেবিলেই ছিল মুরারি, বেয়ারা এসে বলল, এক মহিলা বাইরে বাবুর জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন, ভেতরে আসতে চাইছেন না।
মুরারির প্রথমে সন্দেহ হয়েছিল, মানসীই এসেছে হয়ত। বাইরে এসে সে অবাক, বয়স্কা এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন।
মুরারি নানা রকম সন্দেহ নিয়ে মহিলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। “আপনি আমাকে খোঁজ করছিলেন?”
মহিলা একদৃষ্টে মুরারিকে দেখলেন কিছুক্ষণ। মুরারিও দেখল মহিলাকে। বেঁটে ধরনের গোল চেহারা, গায়ের রঙ ফরসা, তাঁতের সাদা খোলের শাড়ি, মাথায় কাপড়। চোখ মুখ দেখে মহিলাকে কড়া ধাতের মানুষ বলেই মনে হয়।
উনি বললেন, “ও, তুমিই সেই? আমি মানসীর মা।”
মুরারি চমকে গেল। সর্বনাশ! তার মনে হল, লালবাজার থেকে যেন পুলিশ এসে মুরারিকে ধরে ফেলেছে। শুকনো মুখে মুরারি ঢোঁক গিলল। “আজ্ঞে!” মর্মভেদী দৃষ্টি হানলেন মানসীর মা। “আমার মেয়েকে তুমি চেন না?”
“আজ্ঞে হ্যাঁ, দেখেছি।”
“দেখেছ? আর কিছু করোনি?”
কথাটা মুরারির কাছে খুব অশ্লীল ঠেকল। বুঝতে আর বাকি থাকছে না যে, শালা কেদার তাকে ফাঁসিয়েছে। মুরারি ঘামতে শুরু করেছিল। বলল, “আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ-টালাপ আছে।” বলেই মুরারি তার ঘরের দিকে তাকাল, যেন ঘরটা অনেক নিরাপদ। “আপনি ঘরে গিয়ে বসবেন চলুন।”
মানসীর মা মাথা নাড়লেন। “না, আমি এই হট্টগোলের মধ্যে যাব না। লোকজন নেই এমন জায়গায় চলো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।”
মুরারির রাগ হচ্ছিল, কেদার এসে বলবে, মানসীকে একটু ডেকে দিবি চল, তার শাশুড়ি এসে বলবে, তোমার সঙ্গে কথা আছে ফাঁকায় চলো। ব্যাপারটা কী? মুরারি কি জগৎসুদ্ধু লোকের বেগার খাটবার জন্য বসে আছে! অথচ এসব কথা বলা যায় না, অন্তত এই বয়স্কা মহিলার সামনে।
মুরারি বলল, “ফাঁকা জায়গা অফিসে নেই। তবে ক্যানটিনের দিকে যেতে পারেন, এখন হয়ত ভিড় কম।”
মানসীর মা বললেন, “যা করেছ—কেলেঙ্কারি—সেটা তো আর ঢাক বাজিয়ে বলা যাবে না।”
মুরারি আবার কেমন যেন চমকে গেল। মানসীর মা কী ভাবছেন? তিনি কি ভাবছেন, মুরারিই কিছু করে ফেলেছে? যাঃ বাব্বা, কারবার করছে কেদার, আর মুরারির মাথায় সাইনবোর্ড।
ভয়ে ভয়ে মুরারি বলল, “চলুন দেখি, নিচের ক্যানটিনে জায়গা না পেলে বাইরে যেতে হবে।”
মানসীর মাকে নিচে নিয়ে এসে মুরারি একটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে গেল।
মানসীর মা বসলেন।
মুরারি আতিথ্য করে বলল, “একটু চা খাবেন?”
“থাক, যেখানে সেখানে আমরা খাই না। কতরকম ছোঁওয়া ছুঁইয়ি থাকে।”
মুরারি আর অনুরোধ করল না। মানসীর মা মাথার কাপড় সামান্য টেনে নিচু গলায় বললেন, “তোমরা লেখাপড়া শিখেছ, অফিসে চাকরি কর, ভদ্রলোকের ছেলেপুলে, তোমরা গরীব-গেরস্থ বাড়ির এত বড় একটা সর্বনাশ করলে?”
মুরারির আলজিব পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। “আজ্ঞে আমি…।”
“তুমি আমার সর্বনাশ করেছ, এত বড় সর্বনাশ মানুষ তার শত্তুরেরও করে না।”
প্রতিবাদ করে মুরারি বলল, “আপনি কী বলছেন? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না !”
মানসীর মা চোখ রাঙিয়ে ধমক দিলেন, “ন্যাকা, তুমি কিছু বুঝতে পারছ না, ভাজা মাছ উল্টে খেতে জান না। শয়তান সব। পরের বাড়ির মেয়েকে ভুলিয়ে ভালিয়ে এনে সর্বনাশ করে এখন ন্যাকা সাজছ!”
মুরারির চোখমুখ তেতে উঠল। মাথা দপ্ দপ্ করতে লাগল। কোনো রকমে নিজেকে সামলাতে সামলাতে সে বলল, “আপনি নিজের খুশিমত যা মুখে আসছে বলে যাচ্ছেন, এগুলো খুবই অপমানজনক। আমি কোনো ভদ্রবাড়ির মেয়ের সর্বনাশ করিনি।
“আমার মেয়ের সর্বনাশ কে করেছে?”
“আমি? কী বলছেন আপনি?”
“করেছে কে? আমি জানতে চাইছি, কে করেছে?”
মুরারি বেফসকা কিছু বলতে গিয়ে একেবারে শেষ মুহূর্তে সামলে নিল। বলল, “আপনার মেয়ের সর্বনাশ কে করেছে তার জবাব আমি দেব? আপনার মেয়েকেই জিজ্ঞেস করলে পারেন।”
“সে হারামজাদী আর এক কেউটে। কি মেয়েই জন্ম দিয়েছিলাম। বংশের মুখে কালি ঢেলে দিলে গো! তার চেয়ে মরল না কেন, বিষ জোটেনি হারামজাদীর?” মানসীর মা রাগের মাথায় হাতের ঝাপটা দিলেন।
মুরারি রীতিমত ভয় পেয়ে যাচ্ছিল। ঠিক তাদের কাছাকাছি কেউ না থাকলেও তফাতে দু-একজন আছে ; আসছে যাচ্ছে কেউ কেউ। মানসীর মা’র এই গার্হস্থ্য-ভাষণ কারুর কানে গেলে কেচ্ছা হয়ে যাবে।
মুরারি অবস্থাটা সামলাবার চেষ্টা করে বলল, “আপনি অনর্থক আমার উপর রাগ করছেন। আমি কিছু করিনি। বরং ব্যাপারটা যদি বলতেন—”
মানসীর মা বসে বসে হাঁপাতে লাগলেন। মোটা চেহারা, ঘরবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এই রাইটার্স পর্যন্ত ধাওয়া করতে পেরেছেন এতেই তো তাঁর দম ফুরিয়ে যাওয়া উচিত ছিল, তার ওপর এই উত্তেজনা ক্রোধ, ওপর নিচ, মহিলার এখন হার্ট অ্যাটাকও হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।
বসে বসে খানিকটা জিরিয়ে নিয়ে মানসীর মা বললেন, “ব্যাপার আমি কী বলবো? তুমি বলবে।”
“আমি?”
“দেখ বাপু, মিচকিমি করো না। তুমি যাও ডালে ডালে, আমি যাই পাতায় পাতায়। সব আমি খোঁজ পেয়েছি। জানো, তোমায় আমি পুলিশে দিতে পারি?”
ঘাবড়ে গিয়ে মুরারি বলল, “আমায় পুলিশে দেবেন! আমার অপরাধ?”
“তুমি আমার মেয়েকে দিয়ে এই অধর্ম করিয়েছ।”
“আমি?…কী মুশকিল, আপনি ফরনাথিং আমার কাছে এসে ঝামেলা করছেন, আমি আপনাকে বারবার বলছি, আমি কিছু করিনি…।”
“করোনি?”
“না।”
“কেদার কে?”
“আমার নাম কেদার নয়, মুরারি।”
“জানি বাছা, জানি। তোমার নাম ঠিকানা না জেনে কি তোমার অফিসে খোঁজ করতে এসেছি? আমায় অত মুখ্য ভেবেছ?”
মুরারি এতক্ষণে একটু হাঁফ ছাড়ল। যাক্ বাবা, কেদারের নামটা শোনা গেল। এতক্ষণ শালা মনে হচ্ছিল, মুরারি যেন মেয়ে ভাগিয়ে নেবার অপরাধ করেছে।
মুরারি বলল, “কেদার আমার বন্ধু।”
“তোমার প্রাণের ইয়ার। সে হারামজাদা এখানে থাকে না। আসানসোলে থাকে, রেলের চাকরি করে।”
মুরারি চমৎকৃত হল। আগাথা ক্রিস্টির চেয়ে কম কি মহিলা!
মানসীর মা বললেন, “ওই হারামজাদা আমার মেয়েকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বিয়ে করেছে।”
“বিয়ে করেছে?”
“তুমি কিছু জানো না, না? ন্যাকামি করছ? তুমি হলে পালের গোদা! তোমার সব খবর আমি পেয়েছি। তুমি ওদের কানে মন্ত্র দিয়েছ। দাওনি?”
মুরারি বুঝতে পারল, আত্মরক্ষার চেষ্টা বৃথা, মহিলা সমস্ত খবরই জানেন। কথাটা কে ফাঁস করে দিল বোঝা যাচ্ছে না। মানসী নিজেই দিল নাকি? কেদারের কোনো চিঠিপত্র কি মানসীর মার হাতে পড়েছে? অত কাঁচা কাজ কি করবে কেদার? মুরারি কোনো রকম আঁচ করতে পারল না—খবরটা কেমন করে জানাজানি হয়ে গেল। এই জন্যেই বোধ হয় বলে, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।।
নিজেকে বাঁচাবার কোনো উপায় নেই দেখে মুরারি এবার বেপরোয়া ভাবে আক্রমণের পথ নিল। বলল, “আপনার মেয়ে কচি খুকি নয়, কেদারও খোকা নয়, আমার মন্ত্র দেবার তোয়াক্কা তারা করেনি। বিয়ের ব্যাপারটা তারাই ঠিক করেছিল, আমি শুধু রেজিস্ট্রির সময় সাক্ষী ছিলাম।”
“বিয়ে বিয়ে করো না, ওটা বিয়ে নয়।”
“বাঃ বিয়েকে বিয়ে বলবো না? সাবালক ছেলে মেয়ে নিজেরা পছন্দ করে আইনমতে বিয়ে করেছে।”
মানসীর মা চটে উঠে বললেন, “আইনের মুখে আগুন। অমন বিয়ে আমাদের চলে মা।”
মুরারি নিস্পৃহ মুখে বলল, “আপনাদের না চললে আমি কি করব বলুন, আইন আইনই। আপনার আমার করার কিছুই নেই। আপনি না মানলেও আইন তো আপনার মেয়েকে কেদারের স্ত্রী হিসেবেই স্বীকার করবে। চাই কি, কেদারই কোর্ট কাছারি পুলিশ করে তার স্ত্রীকে নিয়ে যেতে পারে আপনাদের কাছ থেকে।”
মানসীর মা কপালে হাত রেখে বসে বসে মুরারির কথা শুনলেন। তাঁর ঠোঁটে পানের রঙ শুকিয়ে খয়েরী হয়ে গিয়েছিল। মস্ত বড় এক নিঃশ্বাস ফেললেন। বললেন, “তোমাকে আর বক্তৃতা করে বোঝাতে হবে না। আমি সবই জেনেছি। তুমি ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে আমার এ শত্রুতা কেন করলে?”
মুরারি কথার জবাব দিল না। জবাব কিই বা আছে। কেদার আর মানসীর ওপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল।
মানসীর মা হঠাৎ বললেন, “তুমি তো নিজে বিয়ে-থা করোনি?”
“না ।”
“তা তুমি বাপু বামুনের ছেলে। বন্ধুর জন্যে দাতা কর্ণ না সেজে নিজেও তো কাজটা করতে পারতে, তবু জাত ধর্ম বাঁচত। যাকগে, মা বাপের দুঃখ বুঝতে পারবে না এখন, পরে বুঝবে, এখন ভাবছ খুব বাহবার কাজ করেছ, ছি ছি।”
মুরারি নীরবে ভৎসনা সহ্য করে নিল। কেদার বেটা যদি শোনে, তার শাশুড়ী মুরারিকে যেচে মেয়ে অফার করতে চেয়েছিলেন বেটা খেপে যাবে।
মানসীর মা চুপ করে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ কেঁদে ফেললেন। শব্দ হল না, চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। মুরারি অপ্রস্তুত, তার ভীষণ অস্বস্তি হতে লাগল। ঘাবড়েও গেল বেশ।
শোক সামলে নিয়ে মানসীর মা আঁচলে চোখ মুছলেন। চোখ দুটি লাল হয়ে গিয়েছে। চোখের পাতা মুছতে মুছতে বললেন, “কেলেঙ্কারী যা হবার হয়েই গিয়েছে। লোক জানাজানি হতেও বাকি নেই। পাড়ায় পাঁচজনে সন্দেহ করছে, আত্মীয়-স্বজন জেনে ফেলেছে। মানসীর বাবা স্কুল থেকে ছুটি নিয়ে নবদ্বীপ চলে গেছেন। এখন বলো আমি কী করি?”
মুরারি এবার খানিকটা সহানুভূতি বোধ করল। বলল, “কি করে লোক জানাজানি হল আমি তো বুঝতে পারছি না। কেদার আসানসোলে থাকে, অ্যাকাউন্টেসি পরীক্ষার পড়া তৈরি করছে। আপনার মেয়ে থাকে কলকাতার বাড়িতে। ওদের মধ্যে কথাই ছিল ব্যাপারটা এখন চাপা রাখবে। দুজনের মধ্যে দেখাশোনাও খুব একটা হয় বলে আমি জানি না।”
“রাখো—রাখো,” মানসীর মা মুখ বেঁকিয়ে বললেন, “দেখাশোনা কম আবার হয় কোথায়! এত বড় বজ্জাত কালকেউটে মেয়ে আমার, আজ ক’মাস ধরেই দেখছিলাম তার হঠাৎ মাসির ওপর দরদ বেড়ে গেছে। ছুটিছাটায় মাসির বাড়ি চুঁচড়ো যাচ্ছি বলে বাড়ি থেকে চলে যেত। তারপর দেখি ফি শনিবার। প্রথমটায় তো বুঝিনি বাবা, সন্দেহও করিনি। ভাবতাম আমার বোনটা বড় একটেরে আছে, যাচ্ছে যাক, আমার বোনঝি রয়েছে, মেয়েরই সমবয়সী। দুজনে বেশ ভাবসাব, ছুটিছাটায় বেড়িয়ে আসুক। পরে ফি শনিবার মাসির বাড়ি রায়না জুড়তেই সন্দেহ হতে লাগল। যেতে না দিলে অশান্তি করত। তা ছাড়া মেয়ের আমার চালচলন ভাল, বাপ মা’র ওপর ভয় ভক্তি রয়েছে, কি করে বুঝব, ভেতরে ভেতরে এত ছিল। ছি ছি, শুনে পর্যন্ত গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করছে।”
মুরারি কৌতূহল বোধ করে বলল, “মাসির বাড়ি ও যেত না?”
“কোথায় যেত। বুড়ি ছুঁয়ে রাখার জন্যে দু-একবার গিয়েছে, তাও বড় একটা রাত কাটাত না। আমার বোনের কাছে খোঁজ করতেই সব ধরা পড়ে গেল।”
“আপনার নিজের বোন?”
“না না, জ্যাঠতুতো বোন, দেখাশোনা বছরে এক-আধবার।”
মুরারির শিস দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করল। শালা কেদার, র্যাটকিলার খুব খেলা দেখিয়েছ। মানসীও তো আচ্ছা, অমন শান্ত, লাজুক, নরম-নরম দেখতে, তার ভেতর ভেতর এত বুদ্ধি! না ; মেয়েদের ওপর দেখে ভেতর বোঝা যায় না।
মুরারি আর পারল না, উঠে গিয়ে এক গ্লাস জল খেয়ে এল।
মানসীর মা বললেন, “এবার বলো, আমি কী করি?”
মুরারি ঘাড় চুলকোতে লাগল। “আমি কী বলব?”
“কেন বাপু, গেরস্থ বাড়ির সর্বনাশ করার সময় বন্ধুর কানে মন্ত্র দিতে পেরেছিলে, আর এখন বলছ আমি কী বলব?”
ঠোক্করটা হজম করে নিল মুরারি, বলল, “আপনি কী করতে চান?”
“আমার তো ইচ্ছে করে বঁটি দিয়ে মেয়েটার গলা কুপিয়ে দি। আর তোমার বন্ধু, সে জোচ্চোরটাকে হাতের কাছে পেলে তার শয়তানি আমি ভাঙতাম।…কিন্তু আমরা তো বুড়ো-বুড়ি হয়ে গিয়েছি। বাড়ির কর্তা সারাটা জীবন আহ্নিক জপতপ করে আর স্কুলে গাধা পিটিয়ে কাটালেন। বাড়িতে আরো তিনটে পোয্য। আমাদের সঙ্গতি কতটুকু, সামর্থ্যই বা কি! মেয়েটারও তো মুখ দেখাতে হবে। সমাজের লোকলজ্জাও বাঁচাতে হবে। আমি বড় দায়ে পড়ে এসেছি। বলো কী করি?”
মুরারির বাস্তবিকই এবার দুঃখ হচ্ছিল। কেদার বোধ হয় এভাবে বিয়ে করে ভাল করেনি। শালা একেবারে উল্লুক, হারামজাদা। মানসীও বা কেমন! রিফিউজ করলে পারত। র্যাটকিলারের প্যাকেট দেখে ভিরমি খেয়ে গেল। প্রেম-ফ্রেম এই জন্যেই এত বাজে।
মুরারি মাথা চুলকে বলল, “আমার তো মনে হচ্ছে, কেদারকে আপনি বাড়িতে ডেকে নিন, না হয় মেয়েকে আসানসোলে পাঠিয়ে দিন।”
“কি কথাই বললে—”, মানসীর মা নাক কুঁচকে বললেন, “—পাড়ায় এমনিতেই কানাঘুষো শুরু হয়েছে, লোকলজ্জায় মরছি, তার ওপর তোমার কেদারকে বাড়িতে এনে বসাই। ও-সব হয় না, আমাদের লোকলৌকিকতা আছে, সমাজ আছে। ওভাবে ফিরিঙ্গি বিয়ে আমাদের হয় না। ওদের আবার বিয়ে করতে হবে, আমাদের চোদ্দ পুরুষে যেমন হয়েছে, সেইভাবে।”
মুরারি চোখ তুলে বলল, “মানে, আপনি বলছেন, আবার টোপর মাথায় দিয়ে কেদারকে বিয়ে করতে যেতে হবে?”
“হ্যাঁ, আমাদের যেমনটি চলেছে এতকাল সেইভাবে।”
“কেদার কি রাজি হবে?”
“না হলে ওর বউ ও পাবে না। তুমি তোমার বন্ধুকে বলে দিও জেদ আমারও আছে?”
মুরারি আর কথা না বাড়িয়ে বলল, “কেদারের সঙ্গে আমার অনেকদিন দেখা হয়নি, তা সে ব্যবস্থা আমি করে নেব। ও যদি রাজি থাকে আপনাকে জানাব।”
“রাজি তাকে হতেই হবে। তুমি ওকে রাজি করাবে। ওকে বলো, মানসীর বাবাকে নয়ত আমি বাঁচিয়ে রাখতে পারব না। ”
মুরারি সামান্য চুপচাপ থেকে বলল, “বেশ, আমি চেষ্টা নিশ্চয় করব। মানসীরও কি তাই ইচ্ছে?”
“তোমার সঙ্গে তো চেনাশোনা আছে। জিজ্ঞেস করে দেখো?”
বোঝা গেল মানসীরও ওই মত।
মানসীর মা শেষ পর্যন্ত উঠলেন। বললেন, “আমাদের ঘরবাড়িতে, পাড়ায় বিয়ের ব্যবস্থা হবে না। অন্য কোথাও ছোট একটু জায়গায় ব্যবস্থা করো। আমাদের ক্ষমতা নেই, সামর্থ্য নেই। সেই বুঝে যা করার করো। আমি আজ চললাম। আবার আসব, কবে আসব মেয়ের মুখে জানিয়ে দিও।”
মানসীর মাকে রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে মুরারি আর অফিসে ফিরল না। মানসীর খোঁজ করতে তার অফিসে চলে গেল।
তিন
পরের শনিবারই নাচতে নাচতে কেদার এল মুরারির অফিসে। ফিটফাট চেহারা মুখ ভরতি হাসি। কেদারকে দেখে মুরারির গা জ্বলে গেল, প্রথম দর্শনেই মুরারি খেপে গিয়ে যাচ্ছেতাই গালাগাল দিল।
কেদার হাসতেই লাগল। “অত রাগ করছিস কেন মাইরি, নে নে সিগারেট খা, চা আনতে বল। বন্ধু লোককে এরকম করতে হয়! তোর কাছে আসতে পারি না, বাট আই অলঅয়েজ রিমেমবার ইউ। তুই একটা জুয়েল, এ ফ্রেন্ড ইনডিড।”
“চুপ কর শালা, আমি তোকে বিলক্ষণ চিনেছি। আমার কাছে এসেছিস কেন?”
“বাঃ বাঃ, মানসী আমায় আর্জেন্ট চিঠি লিখল, তোর সঙ্গে এসে দেখা করতে, তুই বলেছিস মানসীকে।”
“সঙ্গে সঙ্গে তুই আসানসোল থেকে চলে এলি?”
“এলাম, আজ শনিবার।”
“মানসী তোকে আর কিছু লেখেনি?”
“লিখেছে। মানে শুনলুম, তোর কাছে শাশুড়িমশাই এসেছিলেন…এই সব আর কি ।
“শাশুড়িমশাই?”
“আমার শাশুড়িকে মশাই বলাই কি ভাল নয়?”
মুরারি হেসে ফেলল।
চা সিগারেট খেতে খেতে মুরারী মানসীর মার আগমন থেকে প্রস্থান পর্যন্ত সব বিবরণ শোনাল। কেদার কিছু কিছু আগেই মানসীর চিঠিতে জেনেছে। তাকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল।
মুরারি শেষে বলল, “তুই না ওয়ার্ড অফ অনার দিয়েছিলি?”
“কিসের?”
“কিসের? শালা ন্যাকা সাজছিস?”
“ফর গডস্ সেক্, আমি কিন্তু ব্যাপারটা লিক আউট করিনি?”
“কে করেছে?”
“বোধ হয় মানসীর মাসির বাড়ি যাওয়া থেকেই সাম্ হাউ ওরা আন্দাজ করতে পেরেছিল। মানসী মাইরি এত মাসি-মাসি করত! তখনই বলেছিলাম, বেণী মাসির কান কেটেছিল, এই মাসিও তোমায় ডোবাবে…।”
“মানসী মাসির বাড়ি যেত না।”
“যেত না?”
“আবার শালা ন্যাকামি? তুই ওকে টেনে নিয়ে যেতিস!”
একটু চুপ করে কেদার একগাল হেসে বলল, “ভেরি ন্যাচারাল। বউকে টানব এর মধ্যে অন্যায় কী?”
“ভেরি ন্যাচারাল! এখন শালা ন্যাচারাল দেখাচ্ছিস! এরকম কথা কিন্তু ছিল না। তোর কনডিশান ছিল…”
“যা যা, কনডিশান রাখ। নিজে তে শালা বিয়ে করিসনি, কনডিশান দেখাচ্ছিস। একবার রাইট এসটাব্লিশড হয়ে গেলে কে কনডিশান মানে রে? প্র্যাকটিক্যাল বুদ্ধি তোর নেই মুরারি, তুই এখনও সাবালক হোসনি।”
মুরারি জোরে জোরে সিগারেট খেল, হাসল মনে মনে। পরে বলল, “তুই মানসীকে নিয়ে কোথায় যেতিস? থাকতিস কোথায়?”
কেদার বলল, “থাকতাম, থাকবার জায়গা কি পাওয়া যায় না? কত হোটেল-ফোটেল আছে?”
“হোটেলে থাকতিস? থাকতিস কি করে? মানসী তো মাথায় সিঁদুর দেয় না?”
“তুই অত এনকোয়ারি করিস না। বলছি ব্যবস্থা হত, ব্যাস।”
মুরারি কি ভেবে হঠাৎ হেসে ফেলে জিজ্ঞেস করল, “তোরা শালা পকেটে করে বিয়ের রেজিস্ট্রির সার্টিফিকেটটা নিয়ে যেতিস নাকি?”
কেদার মুচকি মুচকি হাসতে লাগল, তার হাসির মমোৰ্ধার অসম্ভব।
মুরারি বলল, “যাক গে, তোদের ধর্ম তোরা করেছিস, এখন বিয়ের কী হবে? ঘরবাড়ি কোথায় পাব, ব্যবস্থাই বা কী করা যাবে?”
কেদার খুব নিশ্চিন্তে সিগারেটে টান দিল চোখ বুজে আয়েস করে। ধোঁয়া উড়তে উড়োতে বলল, “ব্যবস্থা একটা হয়ে যাবে। ভাবছিস কেন।”
“কী ব্যবস্থা হবে সেটাই জানতে চাইছি।”
বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তা দেখাল না কেদার, বলল, “চল না বিকেলে বেরোই, খোঁজাখুঁজি করলে একটা বেরিয়ে যাবে।”
ছুটির পর রাস্তায় নেমে কেদার বলল, “তোর নানুকে মনে আছে?”
“কে নানু?”
“আমাদের সঙ্গে বঙ্গবাসীতে পড়ত, লম্বা মতন দেখতে, মুখে বসন্তের দাগ।”
“ঠিক মনে পড়ছে না, মুখ দেখলে চিনতে পারব। নানুর কথা আসছে কেন হঠাৎ?”
“না, মানে—নানুর সঙ্গে একদিন দেখা হয়ে গিয়েছিল। নানুর ভগিনীপতি শিয়ালদার দিকে নতুন একটা হোটেল করেছে। সুরি লেনের কাছাকাছি। নানু সেখানে প্রায়ই থাকে। হোটেলটায় খদ্দের এখনও তেমন জোটে না। নানুর কাছে গেলে একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারে।”
মুরারি স্পষ্ট করে বন্ধুর মুখ দেখল। কেদারের মুখ দেখে সবই বোঝা যায়। মুরারির আর কিছু জানার দরকার হল না। বলল, “হোটেলে বিয়ে করবি?”
কেদার বলল, “তাতে ক্ষতি কি? আসল বিয়ে তো হয়েই গেছে। এটা জাস্ট লোক দেখানো। মানসীদের পাড়া থেকে সুরি লেন পাক্কা আড়াই মাইল দূরে, আমার শাশুড়িমশাই কিছু বলতে পারবেন না। কম খরচে টোপর পরা, গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে যাবে।”
মুরারি হাঁ করে কেদারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। কেদার যে এত বুদ্ধি ধরে জানা ছিল না মুরারির। বলল, “তোর শাশুড়ি তোকে হারামজাদা বলে, ঠিকই বলে ; বুঝলি, তুই শালা সেন্ট পার্সেন্ট হারামজাদা।”
কেদার কথাটায় কান দিল না। হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে বলল, “আমার শাশড়িমশাইকে বলবি, এটা ভাদ্র মাস, অরক্ষণীয়া কন্যার ভাদ্র মাসে বিয়ে হয়।”
চার
নানুর ভগিনীপতির হোটেলের দোতলার দুই ঘর বরপক্ষ আর কনেপক্ষ ভাগ করে নিল। তেতলার চিলেকোঠার পাশে ছাদনাতলা হল। মুরারির অফিসের রতন হল পুরুত। কেদারকে টোপর পরিয়ে দোতলা থেকে তিনতলায় হাজির করানো হল, মানসীকে কনের সাজ পরিয়ে তেতলায় তুলে আনল প্রণব। মানসীর মা দোতলায় থাকলেন, মাকে নাকি মেয়ের বিয়ে চোখে দেখতে নেই।
রতন তার বাবার পুঁথি আর পাঁজি খুলে খুলে বিয়ের মন্ত্র পড়িয়ে দিল। বামুনের ছেলে হলেও সংস্কৃত ভাষাটা তার মুখে আসে না। যতবার হোঁচট খায়, ততবার একবার করে শালা বলে। মধু বলল, “রতন, তুই কার বিয়ে দিচ্ছিস, তোর শালার নাকি?” হাসাহাসি, পুরুষালী গলায় উলুধ্বনি, মালা বদল, সিঁদুর পরা শেষ করে বিয়ের পর্ব চুকে গেল। আবার দোতলায়। মানসীর মা সামান্য মেয়েলী কাজ সারলেন। কনেপক্ষের একুনে জনা দশেক মাত্র এসেছিল। মানসীর বাবা আসেননি।
কেদার তার শাশুড়িকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই শাশুড়ি বললেন, “এবার বাছা তুমি তোমার বউ নিয়ে যেখানে খুশি যাও, আমার কর্তব্য শেষ হয়েছে।” বলে তিনি কেদারের মাথায় হাত রাখলেন একটু।
কেদার বলল, “আজ্ঞে, আমি ভাবছিলাম, আপনার মেয়ে এখন কলকাতাতেই থাক, আসানসোলে বাড়িটাড়ি খোঁজ করতে দেরি হবে। পরে না হয় নিয়ে যাব।”
মানসীর মা বললেন, “মেয়ে এখন তোমার কাছেই থাকবে। আসানসোলে বাড়ি যতদিন না পাচ্ছ, ওকে চুঁচড়োয় ওর মাসির বাড়িতে রেখে দিও। আমরা অন্য পাড়ায় বাড়ি দেখছি, বাড়ি পাই, তখন একবার মেয়েকে নিয়ে তোমার শ্বশুরমশাইকে প্রণাম করতে এস।”
কেদার নিরীহের মত মুখ করে বলল, “আমার জন্য আপনাদের বড় কষ্ট হল।”
“আর ন্যাকামি করো না, তোমায় আমি খুব চিনেছি।”
কেদার অধোমুখে দাঁড়িয়ে থাকল।
নানুর ভগিনীপতি ইয়ার-দোস্ত টাইপের লোক; হোটেলের খাবার ঘরে কলাপাতা পেতে খুরি গেলাস সাজিয়ে সকলকে খাইয়ে দিলেন।
সব পাট চুকে গেলে মুরারি বিদায় নেবার সময় দেখল, ঝিরঝির করে বৃষ্টি নেমেছে।
কেদার সিগারেট ফুকতে যুঁকতে বলল, “বৃষ্টি নেমে গেল যে রে?”
“তাতে আর তোর কি? তুই তো এখন ফুলশয্যা করবি।”
“দূর শালা, আবার ফুলশয্যে কি? সে সব কবে হয়ে গেছে।”
মুরারি চোখ টিপে বলল, “এই হোটেলে?”
কেদার হাসতে হাসতে বলল, “হোটেল কি রে—এ আমার শ্বশুরবাড়ি, এখানে আমার স্পেশ্যাল ঘর আছে, তক্তপোশ, বিছানা আর একটা আলনা পর্যন্ত—”
মরারি বলল, “সত্যি, তুই একটা জিনিয়স!”
বিয়ের পর মুরারির সঙ্গে কেদারের একবার দেখা হয়েছিল, তারপর আর পাত্তা নেই। মানসীর সঙ্গেও মুরারির দেখা হয় না। একদিন কয়লাঘাটায় গিয়ে খোঁজও করেছিল মুরারি, শুনল—মানসী ছুটি নিয়েছে।
মাস কয়েক পরে আবার এক শীত ফুরিয়ে আসার সময় মুরারি বাড়ি ফিরতেই তার মা বললেন, “ওরে, কেদার এসেছিল।”
“কেদার? কখন?”
“অনেকটা বেলায়, তুই অফিস চলে যাবার অনেক পরে।”
“কী বলল?”
“ও যে কী বলল আমি বুঝতে পারলাম না। ঠাকুরঘরে ছিলাম, বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী-যে বলে গেল হাউমাউ করে, আমার মাথায় ঢুকল না। কিসের একটা কথা তোকে বলতে বলল, আট পাউন্ড করে।”
“আট পাউন্ড?”
“তাই তো বলল।”
হাসতে হাসতে মুরারি ঘরের দিকে পালাল। বেদম হাসি পাচ্ছিল তার। কেদারের বাচ্চা হয়েছে নিশ্চয়। সাবাস কেদার, তুই দেখালি বাবা। কিন্তু, ছেলে না মেয়ে? কেদার কিছু বলে যায়নি। হে ভগবান, ওর যাতে ছেলে না হয়—ছেলে হলেই তো আর একটা কেদার। জ্বালিয়ে মারবে। তার চেয়ে ও শালার মেয়ে হোক, ঠেলাটা বুঝতে পারবে।
রঙ্গলাল
সকালটি বেশ চমৎকার লাগছিল রঙ্গলালের।
সবেই ভাদ্রমাস পড়ল, তাতেই শরৎ-শরৎ ভাবটি ফুটে উঠেছে। ঝকঝকে রোদ, নীলে-সাদায় মেশামেশি আকাশ। সামনের মাঠে অজস্র ঘাস গজিয়েছে বর্ষায়। ওরই এ পাশ ও পাশে মামুলি দু চারটে ফুল গাছ, করবী ঝোপ, কলকে ফুল ; তফাতে এই শিউলি।
জানকী কেবিন থেকে এই মাত্র চা খেয়ে ফিরেছে রঙ্গলাল।
চা আর গরম কুচো নিমকি। খাসা! শেষ সিগারেটটাও। এইবার দাড়ি কামাতে বসবে।
ঘরের মধ্যে বসে দাড়ি কামাতে ইচ্ছে করছিল না। এখনও ঘরের মধ্যে তেমন করে আলো আসেনি। মানে পশ্চিম আর উত্তরমুখো জানলা হওয়ায়, রোদ ঢোকেনি ঘরে, সকালের আলোও ঝাপসা। বেলা বাড়লে অবশ্য এমন থাকবে না।
নিজের মনে ‘কাম সেপ্টেম্বর’-এর শিস দিতে দিতে রঙ্গলাল একটা পুরনো টুল জুটিয়ে নিল। নিয়ে বারান্দায় এনে রাখল। ঢাকা বারান্দা। সামনে মাঠ। বারান্দার এ-পাশটা তার, মানে একটা শোবার ঘর, আর এই বারান্দাটুকু। স্নানটানের ব্যবস্থা ওপাশে। কুয়াতলার দিকে। বারান্দার সিকি ভাগ তার, বাকিটা বাড়িউলির। পুরনো কাঠের কয়েকটা ভাঙা ফাটা তক্তা আর হাত দুই আড়াই চওড়া এক জাফরি উঠিয়ে বারান্দাটিকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে। ভাগাভাগিটা পলকা, মাথায় তেমন উঁচুও নয়।
টুলের ওপর আয়না রেখে রঙ্গলাল তার দাড়ি কামাবার উপকণগুলো নিয়ে এসে সাজিয়ে বসল।
এখন প্রায় আট। দাড়ি কামাতে কামাতে সোয়া আট। তারপর স্নানাদি। সেজেগুজে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়বে কালাচাঁদের হোটেলে। খাওয়া-দাওয়া সেরে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে একটা শেয়ারের সাইকেল রিকশা ধরবে। অফিস পৌঁছতে পৌছতে দশ সোয়া দশ।
কলকাতার ছেলে রঙ্গলাল। নারকেলডাঙায় বাড়ি। গত সাত আট বছর সে কলকাতার হেড অফিসেই ছিল। দিব্যি ছিল। বন্ধুবান্ধব আচ্ছা, সিনেমা থিয়েটার, অফিসের অঞ্জলি, পাড়ার হোমসায়েন্সের রীতা দিদিমণি— একটু শখ শৌখিনতার বান্ধবীদের নিয়ে মনের সুখেই ছিল। শালা ঘোষালসাহেব, উইদাউট এনি ওয়ার্নিং তাকে দুম করে বদলি করে দিল। বলল, ‘সেন, তোমাকে ছাড়া কাউকে ভাবতে পারছি না ইউ নো দ্য জব ভেরি ওয়েল। মাই বেস্ট চয়েস। নপাহাড়িতে আমাদের যে ইউনিট সেখানে তোমাকে পাঠাচ্ছি। ইউনিটটা ছোট, কিন্তু পোটেনশিয়ালিটি প্রচুর। কারখানাটাকে আমরা শিঘ্রি এক্সটেন্ড করব। ওখানের অফিস আর স্টোরে নানা ধরনের ম্যালপ্র্যাকটিস শুরু হয়েছে। তুমি হবে সিনিয়ার অ্যাসিসটেন্ট অফিস আর স্টোরের। তোমায় আমরা লিফট দিচ্ছি। দুটো বেশি ইনক্রিমেন্ট, প্লাস একটা অ্যালাওয়েন্স। উইশ ইউ লাক। আসছে মাসেই চলে যাও।’
রঙ্গলাল বারেন্দ্রি না হলেও বদ্যি। আসলে তো সেনগুপ্ত। সেন বলেই চালায়। সে বুঝতে পারল, ঘোষালসাহেবের সঙ্গে বদ রসিকতা করার ফল এটা। মাত্র কদিন আগে সে এসপ্ল্যানেড পাড়ায় ইভনিং শো শেষ করে, চা-টা খেয়ে সামান্য রাত করই মিনিবাসে বাড়ি ফিরছিল। এমনই কপাল তার সেই মিনিবাসে ঘোষাল ছিল। কোনও মক্কেলের পয়সায় পান-ভোজন বেশিই করে ফেলেছে। ফলে মাতলামির মাত্রাটাও বেশি। ব্যাটা একটা ট্যাক্সি করে চলে গেলেই পারত। তা না করে ভুল মিনিবাসে চেপে মাতলামি শুরু করল। কলকাতার নাইট মিনিবাসগুলো মাতাল-মিনি। তা সে যাই হোক, ঘোষালের মাতলামিতে চটে গিয়ে প্যাসেঞ্জাররা তাকে নামিয়ে দিতে বলছিল কন্ডাক্টাবকে। এই নিয়ে যখন বচসা চরম, তখন পিছনের সিট থেকে রঙ্গলাল বদরকম গলা করে আওয়াজ মারল, ‘ব্যাটাকে কান ধরে নামিয়ে দাও!’…জাত মাতালরা বড় চালাক হয়। ঘোষাল পাদানি থেকে প্রায় পড়তে পড়তে লাফিয়ে উঠল, “কে ব্যা-টা বলল। কে বলল! হোয়ার ইজ দ্যাট ব্লাডি ফাদার! কাম অন। কাম অন রাস্কেল। চলে আয়, আমি মদ খেয়েছি— তোর কী! তুম কোন হো বোলনেওয়ালে।’
মিনিবাসের মধ্যেই রঙ্গলাল ততক্ষণে মুখ লুকিয়েছে।
হলে হবে কী! জাত মাতাল ঘোষাল তাকে চিনে ফেলল।
পরিণাম এই। ট্রান্সফার। কোথায় কলকাতা আর কোথায় এই নপাহাড়ি। তিনশো পঁচিশ কিলোমিটার তফাতে বদলি।
রঙ্গলালদের এখানকার কারখানায় তারকাঁটা তৈরি হয়। বড় কাঁটা, ছোট কাঁটা, তিন মুখ— চার মুখ খোঁচা। মিলিটারিতেও সাপ্লাই যায়।
তা রঙ্গলালের কিছু করার ছিল না। বন্ধুদের শুধু দুঃখ করে বলল, শালা আমায় একবার আগে বলল না, কাঁটায় গেঁথে দিল। ঠিক আছে, আমার নামও রঙ্গলাল। ঘোষালকে আমি দেখে নেব। আর অফিসের অঞ্জলিকে বলল, ‘জম্আ করতে হো কিউ রাকিবোঁ কো, ইক তামশা হুয়া গিলা না হুয়া।’ অঞ্জলি এসব শায়েরির কিছুই বুঝল না।
তা রঙ্গলাল আজ মাসখানেকের বেশি এখানে। এসেছিল যখন তখন ঘন বর্ষা। এখন বৃষ্টিবাদলা একটু কমের দিকে। তবে ভাদ্রমাস বলে কথা! কবে কোনদিন ভাসায় কেউ বলতে পারে না। ভরা ভাদর তো পড়েই আছে।
আসার পর প্রথম মাসটা ‘তারা হোটেলে’ ছিল। তারা মানে ‘নবতারা হোটেল’। এখানে হোটেল মেস নেই বললেই চলে। তারা হোটেলে এক মাসেই রঙ্গলালের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়ায়— অফিসের সিধুবাবু তাকে একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। মানে এই বাড়িটি জুটিয়ে দিয়েছেন দয়া করে। পাড়াটা ভাল, ফাঁকা ফাঁকা, বড়লোকদের উৎপাত নেই, আবার গলিঘুঁজি মাছের আঁশ কুমড়োপচার জঞ্জালও পড়ে থাকে না। মধ্যবিত্ত পাড়া, খানিকটা ছিমছাম ভাবও আছে এখানে।
আজ তিনদিন হল রঙ্গলাল এই বাড়িটায় এসেছে। মানে বাড়ির একটা পাত্তা পেয়েছে। ভাড়া একশো পঁচাত্তর, তিনটে আলো একটা পাখার জন্যে ইলেকট্রিক বাবদ পঁচিশ। মানে দু শোতে হয়ে যাচ্ছে। তক্তপোশ আর টুলের জন্যে অবশ্য ভাড়া গুনতে হয় না। একটা চেয়ার একজোড়া মোড়া রঙ্গলাল নিজেই কিনে এনেছে। খাওয়া দাওয়া বাইরে। জানকীর কেবিনে চা নিমকি জিলিপি সিঙ্গাড়া থেকে মাখন রুটিও পাওয়া যায়। কালাচাঁদের হোটেলটাও ভাল, পরিচ্ছন্ন, যা খাওয়ায় যত্ন করেই পাতে তুলে দেয়। ঘরদোর ঝাটমোছ করার জন্যে একটা বাচ্চা মেয়ে আছে— সরস্বতী।
কলকাতা থেকে আসার সময় রঙ্গলালের মেজাজ যতটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, এখন তার মাত্রা অনেক কমেছে। ভালই লাগছে তার নপাহাড়ি।
টুলের ওপর আয়না জল সাবান সাজিয়ে, সেফটি রেজারে নতুন ব্লেড লাগিয়ে রঙ্গলাল দাড়ি কামাতে বসে পড়েছিল। কোনও তাড়া নেই। কেমন একটা আলসেমিও লাগছিল। দাড়ি কামাতে কামাতে শরৎশোভাও দেখছিল মাঝে মাঝে। না, আর যাই হোক, কলকাতায় এসব পাওয়া যেত না। এমন রোদ, নীল-সাদা মেঘ, পড়ো মাঠ, অল্পস্বল্প বাগান, করবী কলকে…।
রঙ্গলাল গুনগুন করে একটা গানও ভাঁজছিল, আমার রাত পোহাল, শারদপ্রাতে আমার..’, হঠাৎ একেবারে আচমকাই এক চিল চিৎকার। গেল গেল রব তুলে চকিত আর্তনাদ যেন। রঙ্গলালের হাত কেঁপে গেল। লাগল গালে।
“এই যে—শুনছেন। শুনছেন নাকি—” বলতে বলতে জাফরির ফাঁক থেকে কে যেন বলল, “মাঠে একটা গোরু ঢুকে পড়েছে। সব খেয়ে গেল। একটু তাড়িয়ে দিন না।”।
জাফরির ওপারের মুখ এপার থেকে দেখা গেল না স্পষ্ট করে, শুধু চোখ, নাক আর শাড়ির একটা আভাস। রঙ্গলালের তখন পয়লা নম্বর শেভ শেষ হয়েছে, দু নম্বর সাবান লাগানো চলছে গালে।
“একটু তাড়াতাড়ি করুন না! সব যে গেল বাগানের।”
বিরক্ত হলেও রঙ্গলালকে সাবান-লাগানো মুখ নিয়ে উঠতে হল।
এ পাশ থেকে রঙ্গলাল আর ও পাশ থেকে মেয়েটি বারান্দার নীচে নামল। মাঠে।
“ওই যে দেখুন—, দেখুন! এ মা। পটপট করে কচি দোপাটিগুলো এবার খেয়ে ফেলছে!”
রঙ্গলাল গোরুটাকে দেখতে পেল। খয়েরি রং। সাইজ মিডিয়াম তবে গাঁট্টাগোট্টা। শিং আধাআধি। গোরুটা পরমানন্দে যা পাচ্ছে চিবিয়ে যাচ্ছে। কোনও ভূক্ষেপ নেই। অমন সবুজ ঘাস, লতাপাতা!
“যান না একটু তাড়াতাড়ি যান…। এবার ডাঁটাগুলো খাবে। সর্বনাশ হয়ে গেল।”
রঙ্গলাল হ্যাট হ্যাট করতে করতে এগিয়ে গেল।
গোরু নির্বিকার। দোপাটি শেষ না করেই পাশের ছোট সবজিবাগানে কোনও একটা লতানো ডাঁটা চিবোতে শুরু করেছে।
“একটু পা চালিয়ে যান! ইস বাবা, কী পাজি রে!”
পাজি! কে পাজি? গোরু না সে? তবু রঙ্গলাল পা চালিয়ে গোরুর কাছে যেতেই জীবটি মুখ তুলে দেখল। শুধু দেখল না, মুখে সাবান লাগানো মানুটিকে সে অন্য কিছু ভেবে দু কদম এগিয়ে এল। মাথাটায় গোঁতানোর ভঙ্গি।
রঙ্গলাল পিছিয়ে এল। পিছিয়ে এসে হ্যাট হ্যাট করতে লাগল ডান হাত তুলে, যেন এই বুঝি ইট পাটকেল ছুঁড়ে মারবে।
গোরুদেরও বুদ্ধি থাকে। নকল ব্যাপারটা আঁচ করে এবার সে তেড়ে এল প্রায়।
পিছিয়ে গেল রঙ্গলাল। “গুঁতোতে আসছে!”
“আসবেই তো! ঢিল মারুন। ওটা ভীষণ পাজি।”
“কোথায় ঢিল?”
“মাটিতে। দেখুন খুঁজে।”
আশেপাশে কোনও ঢিল দেখতে পেল না রঙ্গলাল। ইটের টুকরো জমানো আছে। একপাশে অবশ্য, কিন্তু কম পক্ষে বিশ গজ দূরে। বাগানের যত্রতত্র হাত বাড়াতে নেই। ইটের গাদায় তো নয়ই। সাপ বিছে— কত কী থাকতে পারে। সময়টাও বর্ষাকাল।
“লাঠি নেই? একটা লাঠি? …স্টিক বা বাঁশ—!”
“খুঁজে আনতে হবে। লাঠি খুঁজে আনতে আনতে বাগান শেষ। ইস্—কী কাণ্ড করছে গোরুটা!”
“ইট পাটকেলওতো পাচ্ছি না।…এই হ্যাট হ্যাট, যাঃ— ভাগ !”
গোরুটা সত্যিই অতি সাহসী ও নির্বিকার। তাড়া খেলেও নড়ে না। নড়লেও অন্য পাশে সরে যায়।
মেয়েটি বিরক্ত হয়ে বলল, “আপনি গোরু তাড়াতেও ভয় পান! আশ্চর্য বাবা !”
গোরুর সঙ্গে রঙ্গলালের নকল একটা লড়াই চলল খানিকক্ষণ, তারপর দু চার টুকরো আধলা ইট পাওয়া গেল।
তাতেই কাজ হল ; গোরু চলে গেল বাগান ছেড়ে।
রঙ্গলালও নিশ্বাস ফেলল।
“ফটকটা ঠিক করে লাগিয়ে দিন ! কে যে এভাবে ফটক খুলে রেখে আসে।” মেয়েটি বলল।
রঙ্গলাল সকালে চা খেতে গিয়েছিল জানকী কেবিনে। ফেরার সময় সে ফটক বন্ধ করেই এসেছে। তবু কথাটা কানে লাগল। অসন্তুষ্ট হল।
ফটক বন্ধ করে দিয়ে এসে রঙ্গলাল বলল, “আমি নয়।”
“তবে চৈতন্যদা। খানিকটা আগে বাজারে গেল!”
“তবে তাই— !” বলে রঙ্গলাল নিজের বারান্দার দিকে পা বাড়াল।
“এই যে শুনছেন। আমি এ-বাড়ির মেয়ে—।”
দাঁড়িয়ে পড়েছিল রঙ্গলাল। দেখল মেয়েটিকে।
মেয়েটি বলল, “সাত আট দিন ছিলাম না এখানে। বড় মাসির বাড়ি গিরিডি গিয়েছিলাম বিয়েতে। কাল রাত্তিরে ফিরেছি। মার কাছে সব শুনলাম।”
“ও!…আমি এখানে দিন তিনেক হল এসেছি।”
“মা বলল। আপনার নাম রঙ্গ!”
“রঙ্গলাল সেন।”
“ওই একই। রঙ্গ। মা রঙ্গ বলল।”
“তোমার কথা শুনেছিলাম। উনি বলেছিলেন। তোমার নাম?”
“ডাকনাম ডুমুর! ভাল নাম, কৃষ্ণা।”
“ডুমুর! বাব্বা, এমন নাম তো আগে শুনিনি। বেশ নাম তো।”
“রঙ্গও আমি শুনিনি।…তবে নতুন নতুন। আয় রঙ্গ হাটে যাই, দু খিলি পান কিনে খাই ; সেই রঙ্গ!” ডুমুর খিলখিল করে হেসে উঠল।
রঙ্গলাল ডুমুরকে দেখল। রোগা ছিপছিপে গড়ন, গায়ের রং শ্যামলাও বলা যাবে না, তার চেয়েও ময়লা। মুখটি একেবারে ঝুরঝুরে। কাটাকাটা। বড় বড় দুটি চোখ। চকচক করছে। নাক একেবারে বাঁশির মতন। ধবধবে দাঁত। এক মাথা চুল, গালে আঁচিল।
ডুমুরের পরনে ছিল ছাপা শাড়ি। হালকা নীল জমির ওপর সাদা হলুদ ফুল-নকশা।
রঙ্গলালের মনে হল, ডুমুরের বয়েস বেশি নয়, হয়তো উনিশ কুড়ি, কি একুশ।
“আচ্ছা, আমি যাই, দেরি হয়ে যাচ্ছে…” রঙ্গলাল আবার পা বাড়াল।
ডুমুর হাসতে হাসতে বলল, “চৈতন্যদা বাড়িতে থাকলে আপনাকে গোরু তাড়াতে ডাকতাম না। ওই গোরুটা ভীষণ শয়তান, পাটনাইয়া, কিছু পরোয়া করে না, নয়ত আমি তাড়িয়ে দিতাম। আমার বড় ভয় করছিল বলে আপনাকে ডাকলাম। তবে কলকাতার লোকরা গোরুছাগল তাড়াতে পারে না দেখলাম।”
ঘাড় ঘুরিয়ে রঙ্গলাল বলল, “আমি তো গোরুছাগল তাড়াবার বাগাল নই।”
“এমা! ছিঃ!” ডুমুর যেন লজ্জা পেয়ে লম্বা করে জিব বার করে দিল।
রঙ্গলাল আর দাঁড়াল না।
দুই
অফিসে দুপুরবেলায় সিধুবাবুর সঙ্গে দেখা রঙ্গলালের। সিধুবাবু বয়েসে বড়। বছর চল্লিশের ওপর বয়েস। ছোকরারা সবাই তাকে সিধুদা বলে। সিধুবাবু কারখানার খোঁজখবর সেরে দুপুরে অফিসে এসে বসে। অর্ডারের কাগজপত্র দেখে।
রঙ্গলাল বলব কি বলব না করে সকালের ঘটনাটা সিধুবাবুকে বলল। রাগ করে বা অপমান বোধ করেছে বলে নয়, এমনি বলল, গল্পচ্ছলে।
সিধুবাবু হেসে বলল, “আরে রাম রাম। আপনি কিছু মনে করবেন না। ডুমুরটা খেপি!।”
“খেপি! মানে খেপা?”
“সেরকম নয়, সেরকম নয়। ওই ওর ধাত। মাথায় ছিট আছে। মেয়ে কিন্তু বড় ভাল। আপনি দেখবেন।”
“তা না হয় বুঝলাম। তবে কথা কী জানেন সিধুবাবু, গোরু তাড়াবার শর্তে একুনে দুশো টাকা দিয়ে আমি ঘরভাড়া নিইনি।”
“ছি ছি, এ কী বলছেন। ছেলেমানুষের কাণ্ড, মাপ করে দেবেন। …আমি বরং একবার গিয়ে বড়দির সঙ্গে দেখা করব। বলব।”
“আরে না না, মশাই! পাগল নাকি আপনি! আমি এমনি বলেছি আপনাকে—কিছু মনে করে বলিনি। ভদ্রমহিলাকে বলতে হবে না।”
সিধুবাবু সামান্য চুপ করে থেকে বলল, “আসলে কী জানেন সেনবাবু, জামাইবাবুর জন্যে ফ্যামিলিটা কেমন ছত্রখান হয়ে গেল। বড়দি আমার নিজের কেউ নয়। ডাকি বড়দি বলে বরাবর। সেই সূত্রে বড়দির স্বামী জামাইবাবু। জামাইবাবু বিচিত্র লোক। এই সেইবার পূর্ণ কুম্ভের মেলায় গিয়ে আর ফিরলেন না। কী হল কী হল করে আমরা যখন উদ্ব্যস্ত, নানান দুশ্চিন্তা, তখন জামাইবাবুর চিঠি এল, তিনি সাধু সন্ন্যাসী হয়ে কুলুমুখীতে যোগীরাজবাবার আশ্রমে বসে পড়েছেন। সাধনভজন করছেন। আর ফিরে আসবেন না সংসারে।”
“সে কী! উনি আর আসেননি?”
“দু বছর আগে একবার এসেছিলেন। চলে গেছেন আবার। তবে চিঠিপত্র ন’মাসে ছ’মাসে দেন।”
“অদ্ভুত মানুষ তো!”
“ডুমুর মেয়েটা তখন থেকে কেমন হয়ে গেছে। খেপি!”।
রঙ্গলাল সামান্য চুপ করে থেকে বলল, “আপনাকে কিছু বলতে হবে না সিধুবাবু। আমি কোনও কমপ্লেন করছি না। বরং, সত্যি বলতে কী— মজাই পেয়েছি। হাজার হোক মেয়েটি ছেলেমানুষ। কত বয়েস হবে?”
“একুশ টেকুশ।”
“সেই রকমই মনে হয়েছিল।….ঠিক আছে, আমি এখন দু-একটা কাজ নিয়ে বসি, পরে কথা হবে।”
সিধুবাবু উঠে গেল।
পরের দিন গোরু এল না। তার পরের দিন আবার একই কাণ্ড। সেই সকালে। এবার একটা নয়, চার পাঁচটা ছাগল ঢুকে পড়েছিল বাগান।
যথারীতি চৈতন্য গরহাজির। রঙ্গলালের ডাক পড়ল। “ও রঙ্গবাবু, শিগগির। ছাগল ঢুকেছে। চার পাঁচটা।”
রঙ্গলাল মাঠে নামল। দুটো বড় ছাগল, তিনটে ছোট। মনে হল, সপরিবারে প্রবেশ। মনের সুখে ফুলগাছ খাচ্ছে। জবাগাছের নীচের দিকের পাতাগুলো শেষ। ছোটগুলো বেলঝাড়ের পাতা চিবোচ্ছে।
ছাগল তো গোরু নয় যে তেড়ে গুঁতোতে আসবে। রঙ্গলাল সহজভাবেই এগিয়ে গেল। “এই হ্যাট—হ্যাট…ভাগ যত্তসব…, যাঃ যাঃ!” হাত তুলে ছাগল তাড়াবার ভঙ্গিতে অনেকটা কাছেই চলে গেল রঙ্গলাল।
হঠাৎ দেখে প্যাঁচানো শিংঅলা একটা বড় ছাগল তাকে দেখছে। দেখতে দেখতে সামনের পা দুটো মাটিতে ঘষে নিল।
দাঁড়িয়ে পড়ল রঙ্গলাল।
“কাছে যাবেন না। ওর কাছে যাবেন না।” ডুমুর পেছন থেকে চেঁচিয়ে বলল, “ওটা ভীষণ বদমাশ ছাগল পেছনের দু পায়ে দাঁড়িয়ে উঠে সামনের পা ছোঁড়ে। মেরে দেবে। অৰ্জনবাবুর ছাগল। ইট মারুন।’’
রঙ্গলাল দু পা সরে এল। “কার ছাগল?”
“মনাক্কা না মরক্কো ছাগল। উঁচু ক্লাস। অর্জুনবাবুর শখের ছাগল।” “উঁচু ক্লাস এখানে কেন?
“ফাঁক পেয়ে পালিয়ে এসেছে। দাঁড়ান আমি লাঠি নিয়ে আসি।”
অর্জনবাবুর ছাগলের সঙ্গে রঙ্গলালের খানিকক্ষণ অ্যাডভান্স রিট্রিট খেলা চলল। ততক্ষণে অন্যরা মুখের সামনে যা পেল মুড়িয়ে দিল।
ডুমুর লাঠি নিয়ে বেরিয়ে এল বাড়ির ভেতর থেকে। বলল, “এই নিন, এটা ছাতার বাঁট। ভাঙা। মারতে যাবেন না, ভয় দেখান।”
ছাগলের দল বিদায় নিল আরও খানিকটা পরে।
ফটক বন্ধ করে দিতে দিতে রঙ্গলাল বলল, “এই ফটকটা সারিয়ে নাও। তিনখানা কাঠ ছাড়া কিছু নেই। বন্ধও থাকে না, ওপরের আংটা একটু ঠেলা মারলেই খুলে যায়।” বলে কম্পাউন্ড ওয়ালের চারপাশটা দেখল রঙ্গলাল। একে ছোট পাঁচিল, তায় ভাঙাচোরা, কত জায়গায় ইট খুলে পড়েছে। ফাঁক হয়ে আছে জায়গাগুলো, সেখান দিয়েও গোরু-ছাগল গলে আসতে পারে।
রঙ্গলাল বলল আবার, “ফটকটা আগে সারাও তারপর পাঁচিলের ভাঙা জায়গাগুলো ঠিক করে নাও, গোরু-ছাগলের উৎপাত থাকবে না।”
ডুমুর বলল, “ও বাব্বা, ফটক সারাতে অনেক টাকা। অত টাকা পাব কোথায়! তার চেয়ে কতকগুলো তক্তা ঠুকে দিলেই হয়ে যায়। আমার গায়ে জোর থাকলে দিতাম ঠুকে। আপনি পারবেন না?”
রঙ্গলাল অবাক। আড়চোখে দেখল ডুমুরকে। কোনো জবাব দিল না।
পা বাড়াতে যাচ্ছিল রঙ্গলাল, ডুমুর বলল, “রাগ করলেন নাকি?”
কোনও জবাব দিল না রঙ্গলাল। কী বলবে ডুমুরকে! সত্যিই মেয়েটা খেপা। তবে খুব সরল। সপ্রতিভ তো বটেই।
বারান্দার কাছে এসে ডুমুর বলল, “চৈতন্যদাকে নিয়ে আমিই কাল ক’টা তক্তা লাগিয়ে নেব। নিজের কাজ নিজে করাই ভাল। আপনাকে লাগবে না।”
রঙ্গলাল হঠাৎ বলল, “এতদিন এই বুদ্ধিটা কোথায় ছিল? আমি আসার আগে গোরু-ছাগল ঢুকত না?”
“রোজ রোজ ঢুকত না। ঢুকলে আমরা তাড়িয়ে দিতাম, চৈতন্যদা আর আমি। চৈতন্যদার পিঠে এখন ফিক ব্যথা, হাত তুলতে পারে না। আর আমার আবার পেরেক ফুটে গিয়েছিল পায়ে বিয়ে বাড়িতে। কী রক্ত কী রক্ত! দেখছেন না, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছি এখনও ব্যথা রয়েছে। যাক গে, পরের একটু উপকার করলে যারা কষ্ঠা পেয়ারার মতন মুখ গোমড়া করে তাদের আমি পায় ধরি না।”
ডুমুর চলে গেল।
হেসে ফেলল রঙ্গলাল।
পরের দিন অফিস থেকে ফিরে ফটক খুলতে গিয়ে রঙ্গলাল দেখল, কাঠের ভাঙা তক্তা, পাতলা কঞ্চি, লোহার তার দিয়ে ফটক মেরামত হয়েছে। অদ্ভুত দেখাচ্ছে ফটকটাকে। সামান্য লজ্জাই হল রঙ্গলালের। হাসিও পেল।
বারান্দার কাছে আসতেই মনোরমাকে দেখতে পেল। ডুমুরের মা। “অফিস থেকে আসছ?” মনোরমা বললেন।
“হ্যাঁ একটু ঘুরে।…আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন?”
“এমনি। আজ বড় গুমোট। ভাদ্দরের গুমোট। বৃষ্টি হবে।”
“মনে হচ্ছে। আকাশটা থম মেরে আছে। …ডুমুর কোথায়?”
“ঘুমোচ্ছে!”
“এই সন্ধের মুখে ঘুমোচ্ছে !”
“সারা দুপুর চৈতন্যকে নিয়ে বসে বসে ফটক সারিয়েছে। কী ছাইভস্ম করেছে কে জানে! কথা তো শোনে না। ভাদ্দর মাসের দুপুর মাথায় নিয়ে কেউ ওভাবে বসে থাকে! এখন মাথা ব্যথায় মরছে। জ্বরজ্বালা না হলেই বাঁচি।”
রঙ্গলাল কেমন কুণ্ঠা বোধ করল। বলল, “বাগানে রোজ গোরু-ছাগল ঢুকে পড়ে।”
‘বাগানের আছে কী! মরা বাগান। দুটো ঘাস আর ঝোপঝাড়ের জঞ্জাল। বর্ষায় একরাশ আগাছা জন্মেছে। না হয় গোরু-ছাগল ঢুকে দুটো আগাছা খেত।”
রঙ্গলাল কিছু বলল না।
“তুমি ভাল আছ তো?”
“হ্যাঁ, মোটামুটি ভালই।…আমি চলি।”
“এসো।”
বৃষ্টি এল আরও খানিকটা পরে। তুমুল বৃষ্টি। আজ সারাদিনই ভীষণ গুমোট গিয়েছে। বৃষ্টি নামায় যেন গা জুড়োল।
রঙ্গলাল একটা ব্যবস্থা করে নিয়েছিল কালাচাঁদ হোটেলের সঙ্গে। রাত্রে সে আর খেতে যেত না হোটেলে, কালাচাঁদের ওখানে কাজ করে—একটা ছেলে এসে খাবার পৌঁছে দিয়ে যেত রঙ্গলালকে। টিফিন কেরিয়ারে। সকালে সরস্বতী সব ধুয়ে মুছে বাড়ি যাবার পথে হোটেলে ফেরত দিয়ে যেত।
এত বৃষ্টিতে হোটেল থেকে লোক আসা মুশকিল। তবে রাত এখন বেশি নয়, আটটা। ঘন্টাখানেক ধরে আরও যে বৃষ্টি হবে তা মনে হয় না। থেমে যাবে। কালাচাঁদের হোটেলও তেমন দূর নয়।
রঙ্গলাল কী করবে কী করবে ভাবতে গিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে বাড়িতে চিঠি লিখতে বসল। বউদিকেই লিখবে। আগের বার মাকে লিখেছিল। বউদি নিশ্চয় চটে আছে। ভাইপোটা কী করছে কে জানে! সাত বছর বয়েসেই সে শোলের আমজাদ খান।
সবে বিছানায় গুছিয়ে বসে রঙ্গলাল চিঠি লেখার প্যাডটা টেনে নিয়েছে—এমন সময় ঝপ করে সব চলে গেল। আলো পাখা। একেবারে অন্ধকার। চোখে কিছু ঠাওর করা যায় না। এখানে আলো যাওয়া মানে ঘণ্টা দেড় দুইয়ের ব্যাপার। টর্চ আর মোমবাতি রাখতেই হয়। কিন্তু এই মুহূর্তে কোথায় যে টর্চ রাখা আছে—কোথায় বা মোমবাতির টুকরো, খুঁজে পাওয়া মুশকিল।
অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিতে লাগল রঙ্গলাল।
সামান্য পরে বিছানা ছেড়ে উঠে হাতড়ে হাতড়ে টর্চটা পেল। কিন্তু মোমবাতির টুকরোটা শেষ। নতুন আর কেনাও হয়নি। ভুলে গিয়েছে। টর্চ জ্বেলে কতক্ষণ বসে থাকা যায়!
বৃষ্টি জোরেই পড়ছে। একটা জানলা আধাআধি খোলা। বিদ্যুতের ঝলকানি চোখে পড়ছিল। বাতাসও ঠাণ্ডা।
টর্চ জ্বেলে জানলার কাছে গিয়ে বাইরেটা দেখার চেষ্টা করল। জল আর জল, আতাঝোপে পাতায় বৃষ্টির ঝাপটা লেগে সব দুলছে।
ফিরে এল রঙ্গলাল। বিছানাতেই বসল আবার। টর্চ জ্বালিয়ে অকারণ ব্যাটারি খরচের কোনও মানে হয় না। তার চেয়ে অন্ধকারে বসে থাকাই ভাল।
একলা অন্ধকার ঘরে বৃষ্টির মধ্যে বসে থাকতে থাকতে তার গান এসে গেল। রঙ্গলাল প্রথমে নিচু গলায় সামান্য রিহার্সাল দিয়ে নিয়ে ক্রমশই গলা চড়িয়ে গাইতে লাগল : ‘এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘন ঘোর বরিষায়…।’
রঙ্গলাল একটু আধটু গাইতে পারে। গাইতে পারে বলে অফিস থিয়েটারে মাঝারি গোছের একটা পার্টও পেয়ে যায়। সেবার তো স্টেজে ‘ব্যাপিকা বিদায়ের’ গান গাইতে গাইতে ঘোষালের কোমরে এক গুঁতোই মেরেছিল। কেন মারবে না! ওই শালা ঘোষাল হিরোইন অঞ্জলিকে আজেবাজে জায়গায় টাচ করছিল।
গান গাইতে গাইতেই রঙ্গলাল শুনল, বারান্দার দিক থেকে গলা ফাটিয়ে কে যেন চেল্লাচ্ছে।
গান থেমে গেল রঙ্গলালের। তাড়াতাড়ি টর্চ জ্বালিয়ে বারান্দায় এল।
“কে?”
“আমি। দেখুন তো আপনার বারান্দায় সাপ ঢুকল নাকি?” জাফরির ফাঁক থেকে ডুমুর বলল। তার হাতে লণ্ঠন।
“সাপ! বারান্দায়!” রঙ্গলাল লাফিয়ে উঠল।
“দেখুন আগে।”
টর্চের আলো ফেলে ফেলে বারান্দা দেখল রঙ্গলাল। সাপ দেখতে পেল না, তবে ব্যাঙ উঠে পড়েছে দু একটা মাঠ থেকে। আগেও উঠেছে। সিঁড়ি দিয়ে লাফাতে লাফাতে দিব্যি উঠে আসে।
“কই, সাপ তো নেই”—রঙ্গলাল ভয়ে ভয়ে বলল।
“তা হলে ঘরটা দেখুন।”
“ঘর! কী সর্বনাশ।”
“দেখুন আগে।”
“তুমি সাপ দেখলে কোথায়?”
“বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি। হঠাৎ দেখি একটা সাপ সরসর করতে করতে পাশের বারান্দায় চলে গেল।”
সাপে রঙ্গলালের ভীষণ ভয়। কলকাতায় সে যেসব সাপ দেখেছে সেগুলো বেদেদের ঝুড়ি থেকে মুখ বাড়ায়, বাঁশির সুরে দোল খায়। আসল সাপ সে দেখেনি। চিড়িয়াখানাতেও সে সাপের দিকে পা বাড়ায় না।
রঙ্গলাল বলল, “ঘরে আমার মোমবাতিও নেই। একেবারে অন্ধকার। টর্চ জ্বেলে জ্বেলে ঘরের কোথায় সাপ খুঁজব!”
“টর্চ দিয়েই দেখুন! তাতে ভাল দেখা যায়।”
“দেখতে গিয়ে যদি কিছু হয়ে যায়। সাপে আমার ভীষণ ভয়। সাপ শুনেই গায়ে কেমন করছে! সিরসির।”
“কী লোক রে বাবা! গোরুতে ভয়, ছাগলে ভয়, সাপে ভয়। ভয়ের পুঁটলি!” “আলো যে নেই! কী করব!”
“জ্বালাতন! কলকাতার বাবু!.আসছি আমি—”
ডুমুর বাহাদুর মেয়ে! ওই বৃষ্টির মধ্যে হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে বারান্দার সিঁড়ি টপকে ভিজতে ভিজতে এপাশে চলে এল। বৃষ্টি বাঁচাতে মাথায় একটু কাপড় তুলেছিল।
ঘরে এসে ডুমুর লণ্ঠনের আলোয় ঘরটা ভাল করে যেন দেখে নিল। “না, দেখতে পাচ্ছি না। ও তবে মাঠেই নেমে গেছে।’’
রঙ্গলাল নিশ্চিন্ত হল। “সাপ তুমি দেখেছিলে?”
“না দেখলে বলি?”
“কী সাপ? বিষাক্ত!”
“বা রে মশাই, আমি কেমন করে জানব! হতে পারে বিষাক্ত!”
“মহা মুশকিলে পড়া গেল! এখানে সাপও আসে।”
“মেঠো জায়গায় বর্ষাকালে সাপ আসবে না।”
“আমার হয়ে গেল। ঘুম বন্ধ।”
“ঘুম বন্ধ কেন! কাল খানিকটা কার্বলিক অ্যাসিড ছড়িয়ে দেব। সাপ আসবে না। অ্যাসিডের গন্ধ ওরা সহ্য করতে পারে না।”
কী মনে করে রঙ্গলাল বলল, “তুমি না মাথার যন্ত্রণা নিয়ে শুয়েছিলে বিছানায়, হঠাৎ বৃষ্টির মধ্যে বারান্দায় এলে কেন?”
“বা রে! মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল তো কী হল! মার একটা ওষুধ খেলাম। যন্ত্রণা কমে গেল। গা মুখ ধুয়ে চা খেলাম, বৃষ্টি এল। কী সুন্দর বৃষ্টি। আলো নিয়ে বারান্দায় এলাম একবার বৃষ্টি দেখতে। কানে গেল, কে একটা চেঁচাচ্ছে। বারান্দার এপাশে এসে কান পেতে শুনি আপনি গান চড়িয়েছেন…”
রঙ্গলাল থতমত খেয়ে গেল। “গান চড়িয়েছি মানে?”
“ওই হল!…দম না থাকলে পুরনো রেকর্ড চাপালে ওই রকম শব্দ হয়।”
“আচ্ছা! তুমি গান জান?”
“না। নকল করতে জানি।”
“শুনি তো একটু নকল।”
“না। আপনার ঘরে বসে আমি রাত্তির বেলায় গান গাইব কেন? আমি অসভ্য?”
রঙ্গলাল হেসে ফেলল। পরে বলল, “আমি তোমায় অসভ্য বলেছি। তুমি খুব সভ্য। দারুণ। …বেশ, কাল সকালে না হয় মাঠে দাঁড়িয়ে গান শুনিয়ে দিও।”
ডুমুর ঘাড় হেলিয়ে বলল, “কালকের কথা কাল, যদি পড়ে তাল বড়াভাজা খাবে জাদু এখন খাও গাল…”
রঙ্গলাল হো হো করে হেসে উঠল।
ডুমুর বলল, “আমি যাই। আলোটা থাকল। …একটা লণ্ঠন কিনে আনবেন মশাই কাল, মোমবাতিতে কিছু হয় না।”
“তাই দেখছি।…কিন্তু সাপ! সেটা কোথায় গেল?”
“নিজের জায়গায় চলে গেছে। আর যদি কামড়ায় কী হবে! পায়ে দড়ি বেঁধে দেব। এখানে শিশিরজেঠা ভাল ইনজেকশান দেয় সাপের। পটাপট দু চারটে দিয়ে দেবে। মরবেন না।”
আলো রেখে চলে যাচ্ছিল ডুমুর। রঙ্গলাল বলল, “দাঁড়াও।” বলে আলো হাতে করে তাকে সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিল।
“সাপ কামড়ালে তোমায় কিন্তু ডাকব”, রঙ্গলাল হাসতে হাসতে বলল।
তিন
রঙ্গলালের সঙ্গে ডুমুরের ভাবসাব জমে গেল। এখন দুজনে গল্পগুজব হয় নানারকম। বাড়ির গল্প, নিজেদের গল্প। হাসিতামাশা। আবার অন্য গল্পও হয়। যেমন ডুমুরের বাবার গল্প। বাবাকে ডুমুর পছন্দ করে না। একটা বয়স্ক মানুষ কুম্ভমেলায় গিয়ে রাতারাতি ভোল পালটে ফেলল কেমন করে ডুমুর ভাবতেই পারে না! সাধু সন্ন্যাসী হওয়া অত সহজ! হাজারটা সাধুর মধ্যে ন’শো নিরানব্বইটা হল ‘ভেকধারী’, খায়-দায় গাঁজা চড়ায় আর বগল বাজায়। বাবা স্বার্থপর ; মাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে। এ-বাড়ি কি বাবার নাকি? দিদিমার বাড়ি—মা পেয়েছিল। বাবা তো চুনসুরকি ইটের দোকান করতে করতে একদিন পালিয়ে গেল। যাবার সময় মায়ের ছ’গাছা চুড়ি আর একটা হার নিয়ে পালিয়েছে। … ভাগ্যিস—দিদিমার কিছু টাকাপয়সা মায়ের নামে জমানো ছিল, নয়ত—ডুমুররা না খেয়েই মরত।
রঙ্গলাল ডুমুরের রাগারাগি বেশি বাড়তে দিত না। বাবার কথা থেকে অন্য কথায় চলে যেত বুদ্ধি করে।
“তুমি লেখাপড়া করলে না কেন?”
“করেছি তো। স্কুল শেষ করে আর করিনি।”
“কলেজে?”
“কলেজে নলেজ বাড়ে? ছাই বাড়ে! আসুন না আপনি আমার সঙ্গে অংক কষতে, মশাইকে আমি ঘোল খাইয়ে দেব।” ডুমুর আজকাল রঙ্গলালকে ‘রঙ্গদা’ বলে। মাঝে মাঝে তুমিও হয়ে যায়।
রঙ্গলাল হেসে বলল, “আমি এম কম পাস তা তুমি জান?”
“মাস্টারগিরি রাখুন। আমি ছেলেবেলা থেকে অনেক মাস্টার চিবিয়েছি।” বলে ইশারায় বই দেখাল—মানে অংকের বই। আবার বলল, “মুখে মুখে এক মিনিটে একটা হিসেবের অংক করে দিতে পারেন? তিন হাজার তিনশো তিরানিব্বই, প্লাস পাঁচ হাজার পাঁচশো পঞ্চান্ন, ইন্টু ন হাজার ন’শো নিরানব্বই মাইনাস এক কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ তিরিশ হাজার চারশো ছেচল্লিশ হলে—তোমার অংকফল কী হবে?”
রঙ্গলাল মাথা নাড়তে নাড়তে হেসে বলল, “মুখে মুখে পারব না, কাগজ কলম নিয়ে বসতে হবে।”
“এই বুদ্ধি! পাস! কাঁচকলা।”
“যা বলেছ! কাঁদি।”
“আচ্ছা সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি, চারটে চুম্বক এক জায়গায় রাখা আছে। এক কথায় কী বলা যাবে চারটে চুম্বককে? চৌচুম্বক, চুচুম্বক না চতুর্চুম্বক?”
রঙ্গলাল অট্টহাস্য হেসে ফেলল। বলল, “জানি না।”
“আচ্ছা আর-একটা প্রশ্ন। আকাশে পাশাপাশি দুটো তারা একটা থেকে অন্যটা কত দূরে থাকে।”
রঙ্গলাল এবার অবাক হল। এরকম প্রশ্ন তো ডুমুরের করার কথা নয়! সে নিজেও কোনওদিন করতে পারত না। বলল, “তোমার মাথায় হঠাৎ আকাশের তারা এল কেন?”
“বাঃ, আসবে না! আকাশের তারা দেখলে মনে হয় না, কত গায়ে গায়ে রয়েছে। তা বলে তাই কি থাকে! একটা থেকে আরেকটা হয়তো লক্ষ লক্ষ মাইল দূর।”
রঙ্গলাল বলল, “তুমি এসব পড়?”
“এ তো ছেলেবেলা থেকে পড়েছি।…আমাদের বাড়িতে দাদু-দিদিমার রেখে যাওয়া অনেক পুরনো কাগজ আছে। বাঁধানো কাগজ। কত পত্রিকা উই খেয়ে শেষ করে দিয়েছে। এখনও দেড় দু আলমারি আছে!”
“যা চ্চলে। আমায় তো বলবে একবার। আমি এখানে একটাও বই পড়তে পারি না। শুধু বাসি খবরের কাগজ।”
“তা জানব কেমন করে! মুখ দেখে?” ডুমুর মুচকি হাসল। কী পড়বেন? ষণ্ডার ঘাড়ে গুণ্ডা?”
“যাঃ। ফাজলামি কোরো না।”
“ফাজলামি কেন! দিনেন রায়ের লেখা। বেশ, ‘মেসোপটেমিয়ায় প্রথম বাঙালি’ পড়বেন?”
“না।”
“তা হলে একটা উপন্যাস পড়তে পারেন, ‘ঝড়ের পাখি।’ মেয়ের লেখা। না হয় ‘পরশমণি’।”
রঙ্গলাল বলল, “যা হয় দিও।সময় কাটলেই হল।”
“ঠিক আছে এনে দেব।” …আগে ‘লুলু’-টা পড়ুন।”
“লুলু?”
“আজ্ঞে হ্যাঁ, ‘লুলু’। …নগেন গুপ্ত।”
“তাই দিও।”
সত্যিই ডুমুর একটা করে পুরনো বাঁধানো পত্রিকা এনে দিতে লাগল রঙ্গলালকে। ভাদ্রমাস শেষ হয়ে আশ্বিনের মাঝামাঝি চলছে।
সামনে পুজো।
রঙ্গলাল সকালে কিছু জামা প্যান্ট মাটিতে ফেলে সরস্বতীকে বলছিল, এই যাবার সময় এগুলো ধোপার বাড়িতে দিয়ে যাস। বলবি আসছে হপ্তায় দিতে। বাবুর দরকার।
এমন সময় ডুমুর এল। হাতে চায়ের কাপ। আজকাল সে মাঝে মাঝে সকাল সন্ধেতে রঙ্গলালকে চা এনে দেয়। নিজেদের চা হয় যখন তখন বাড়তি এক কাপ তৈরি করে নেয়। মনোরমাই হয়তো বলে দিয়েছেন।
চা রেখে ডুমুর বলল, “আপনি বালতি তুলতে পারেন?” রঙ্গলালকেই বলল, সরাসরি।
“বালতি?”
“কুয়ায় বালতি পড়ে গেছে।”
“কেমন করে?”
“দড়ি ছিঁড়ে। পারেন তুলতে?”
“কেমন করে তুলব। আমি কি কুয়ার মধ্যে নামতে পারি?”।
“না মশাই বালতি তুলতে কুয়ায় নামতে হয় না। কলকাতার বাবুলোক—কিছুই জানেন না। বালতি তোলার কাঁটা আছে। কাঁটা দিয়ে তুলতে হয়।”
“ও। তা চৈতন্য..”
“তার জ্বর। জ্বর হয়ত একশো, কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে—আর ভবতারার গান গাইছে।’’
রঙ্গলাল চা খেতে খেতে বলল, “তুমি যদি দেখিয়ে দাও—আমি একবার ট্রাই করতে পারি। আমার আবার অফিস। তবে আজ শনিবার। দুপুর দুপুর ছুটি। বিকেলে অনেক সময় পাব।”
“তা পাবেন। তবে তখন অন্ধকার হয়ে আসবে।”
“আরে না না, অত অন্ধকার হবে না। আমার চোখ খুব ব্রাইট। দারুণ ভিশন। তবে তোমার চোখ আরও ঝকঝকে।”
ডুমুর আড়চোখে দেখল রঙ্গলালকে। মুচকি হাসল। “দেখা যাক।”
বিকেলের গোড়াতেই রঙ্গলাল ডুমুরকে নিয়ে কুয়াতলায় বালতি তুলতে গেল। দড়িতে অন্য একটা বালতি বাঁধা। বালতি খুলে ভারি কাঁটাটা বাঁধল। তারপর ঝুঁকে পড়ল। এমন সময় বৃষ্টি এল। আশ্বিনের বৃষ্টি। হঠাৎ এল এবং জোরেই। কুয়াতলার পাশে কলাগাছের পাতায় বৃষ্টি পড়ার শব্দ। হরীতকী গাছের পাতা উড়তে লাগল। দেখতে দেখতে ঘোর হয়ে গেল আকাশও।
রঙ্গলালদের পালিয়ে আসতে হল। দু’জনেই ভিজে গিয়েছে। জামা পাজামা শাড়ি লেপটে রয়েছে শরীরে।
ডুমুর নিজেদের দিকে চলে গেল। রঙ্গলাল তার ঘরে।
জামাটামা বদলাবার সময় রঙ্গলালের ভালই লাগছিল। কুয়াতলার পারে শুয়ে বুক ঝুঁকিয়ে কাঁটা নিয়ে সে যেন চমৎকার এই খেলা শুরু করেছিল। পাশে ডুমুর। মাথার ওপর আশ্বিনের আকাশ কখন আচমকা মেঘ এনে দিল বৃষ্টি নামিয়ে। এ একেবারে ঝাপটা মারা এলোমেলো বৃষ্টি, যেন দোলনায় দুলে আসছিল বৃষ্টি, এই এল, গেল, আবার এল। কলাগাছের সবুজ পাতাগুলোও দুলে দুলে উঠছিল।
বৃষ্টি থামল। সন্ধে হল।
ডুমুর এল আরও খানিকটা পরে। মাথার চুল পিঠে ছড়ানো। ভেজা চুল তো আর বিনুনি করে রাখা যায় না। পরনে ডুরে শাড়ি। গায়ের জামাটা সাদা।
“এই যে মশাই নিন, গ্লাসে করে এনেছি। মা বলল, আদার রস দিয়ে করে দে, অবেলায় আশ্বিনমাসে বৃষ্টিতে ভিজেছে। জ্বরজ্বালা হতে পারে। নিন, আদা গোলমরিচ চায়ের মিক্সচার খান। ঘোড়া মিক্সচার।’’
চা নিল রঙ্গলাল। “তুমি খাবে না?”
“না। আমি এমনি চা খেয়েছি।”
“জ্বরজ্বালা তো তোমারও হতে পারে।”
“দূর, আমাদের শরীর অত পলকা নয়। গরিবের শরীর। দরকার পড়লে বাসন মাজতে হয়, ঘর ঝাঁট দিতে হয়…”
“ও, অ-পলকাদের জ্বর হয় না?”
“হলে শুয়ে পড়ে থাকব। আপনাকে তো আবার পুজোর ছুটিতে কলকাতায় যেতে হবে। জ্বর হলে যাবেন কেমন করে?”
“যাবার এখন আট দশদিন বাকি! বাঃ, দারুণ হয়েছে তো! থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। বসো৷”
“কত দিনের ছুটি আপনার?”
“দিন দশেক।’’
“পূর্ণিমা পর্যন্ত।”
“হ্যাঁ। আগেই তো বলেছি তোমায়।”
মোড়ায় বসে পড়েছিল ডুমুর। মাঝে মাঝে হাত দিয়ে মাথার এলানো চুল ছড়িয়ে ফাঁক করে নিচ্ছিল।
“তোমাদের পাড়াতেও তো পুজো হচ্ছে প্যান্ডেল বাঁধছে দেখলাম।” “বরাবরই হয়।”
একটু চুপচাপ। তারপর রঙ্গলাল বলল, “কাল রবিবার। কাল একবার সকালে ট্রাই করব। পারব মনে হচ্ছে।”
“পারবেন না। কাঁটা দিয়ে ডোবা বালতি তোলা অত সহজ নয়! এলেম চাই। পশুপতিকে খবর দেব। তুলে দিয়ে যাবে। ওরা পারে। ওদের কাজ।”
“চেষ্টা করে দেখি…।”
“দেখতে পারেন। আপনার মুরোদে কুলোবে না।”
রঙ্গলাল চায়ের গ্লাস নামিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। তুলে নিল আবার গ্লাস। হাসল। “আমার মুরোদ সম্পর্কে তুমি সবজান্তা হয়ে গেছ?”
ঘাড় হেলিয়ে দিল ডুমুর। “আধজান্তা হয়েছি।”
“কথায় তুমি খুব পাকা।”
“আজ্ঞে, বয়েস তো কম হল না। আপনার মতন পেটভরা বিদ্যে না থাক—একটু মাথা তো আছে।”
রঙ্গলাল হাসতে হাসতে বলল, “মাথা তোমার আছে। তবু মাসিমা বলেন, ও কেমন পাগলি মেয়ে। বিধুবাবু বলেন, খেপি।”
“জানি। মুখ আছে, বলে। আমিও তো বলতে পারি…”
“কী?”
“বাদ দিন ওসব।” ডুমুর সামান্য চুপ করে থাকল। হাঁচল বার কয়েক। আঁচলে নাক চেপে থাকল দু মুহূর্ত। তারপর বলল, “কই, দাবা খেলবেন না?”
‘না। আজ আর ভাল লাগছে না। দাবাটা আমার মগজে ঢোকে না। তুমি ভালই পার।”
“মগজে কী ঢোকে!”
“আর সব ঢোকে।…আমি ক্রিকেট খেলতে জানতাম, তবলায় ঠেকা দিতে পারতাম, নাটক করেছি অফিস ক্লাবে—। তাসটাও জানি। ভালই জানি।” “ওরে বাবা, অনেক গুণ। গানও তো গাইতে জানেন।”
“খারাপ নয়, সে তুমি যাই বলো।”
“নমুনা তো পাই মাঝে মাঝে,” ডুমুর হাসল। “পরশু সকালে কী একটা যেন গাইছিলেন গলা চড়িয়ে।”
“কবে? পরশু? পরশু সকালে।…দাঁড়াও মনে করি?…হ্যাঁ, মনে পড়েছে— একটা গজল গাইছিলাম : ‘ইয়ে জান তুম না লোগে তো ইয়ে আপ জায়েগি। ইস বেবফা কি খ্যয়ের কঁহা তক্ মানায়েঁ হুস্!’ আমার গলাটা স্লাইট ভাঙা ভাঙা একটু নাকি নাকি করে গাইলে গজলে দারুণ সুট করে যায়।”
“তাই বুঝি! তা মানে কী মশাই জান তুম না লোগে না কী যেন বললেন?”
“মানে আছে। তবে বাংলায় বললে এর রস নষ্ট হয়ে যায়…। আরবি, ফারসির ব্যাপারটাই আলাদা…গজল ঠিক বাংলায় হয় না।”
“মানেটা বলুন না।”
“মানে—মানের জন্যে কেউ গান গায়! মানেটা শুনে—’’
“শুনি!”
রঙ্গলাল কেমন অস্বস্তিতে পড়ে গেল। তারপর আমতা আমতা করে নিচু গলায় বলল, “মানে হল, মানে একজন লাভার বলছে এই প্রাণ আমার তুমি যদি না নাও তবে সে নিজেই আমাকে ছেড়ে যাব! মানে, আমি ডেড। ইস বেবফা কী খ্যয়ের…”
“বারে”, ঠোঁট কেটে ডুমুর বলল, “না নিলে প্রাণ ছেড়ে যাবে! কোথায় যাবে? খাঁচায় না মাচায়, আকাশে না মাটিতে?” বলে হি হি করে হেসে উঠল।
রঙ্গলাল একেবারে অপদস্থ। কথা আসছিল না! দূর শালা, বাংলায় কি ইয়ে জান তুম না লোগে গাওয়া যায়? শরিফ মিয়ার গলায় গানটা শুনলে বুঝতে পারত ডুমুর এই গানের কী ডেপথ, কী রকম এক্সটেনসান অফ সরো, কী প্রচণ্ড আকুলতা।
নিজেকে সামলে নিয়ে রঙ্গলাল বলল, “হেসে সব জিনিস উড়িয়ে দিয়ো না মিস ডুমুর। এবার আমি কলকাতা থেকে ফেরার সময় আমার টেপ রেকর্ডার আর গজলের ক্যাসেট নিয়ে আসব। তখন শুনবে। রেকর্ডার খারাপ হয়ে আছে আনতে পারিনি। আমি যদি প্রিপেয়ার হয়ে আসতাম—তোমায় শুনিয়ে দিতাম।”
ডুমুর হাসতে হাসতে বলল, “ক্যাসেট আনবে তো। এনো! প্রাণ তো আনবে না “ ডুমুর নিজের অজান্তেই তুমি বলে ফেলল।
চার
লক্ষ্মীপুজোর পরের দিনই রঙ্গলাল কলকাতা থেকে ফিরে এল।
এবার অনেক জিনিস গুছিয়ে এনেছে। শীত সামনে বলে গরম পোশাক কিছু, তার শখের টেপ রেকর্ডার, যেটা সারাতে দেওয়া ছিল বলে আগের বার আনতে পারেনি, একগাদা ক্যাসেট, নিজের ক্যামেরা, এমন কি একটা চার সেলের চৌকো টর্চ, কয়েকটা থ্রিলার বন্ধুবান্ধবদের হাত ফেরতা।
ফিরে এসে দেখল, ডুমুর নেই। কোথায় গেল?
মনোরমা বললেন, আর বোলা না, আমার বড় বোন আর বোনঝিরা কিছুতেই ছাড়ল না। গিরিডি গিয়েছে। দ্বাদশীর দিন। বড় বোনঝির বিয়ে হয়েছে গত শ্রাবণে। তখন গিয়েছিল ডুমুর। এবার টেনে নিয়ে গিয়েছে নতুন জামাই, মেয়ে পুজোর সময় এসে রয়েছে ওখানে। দু-চার দিন হইচই করবে সবাই মিলে তাই। আমি আর কেমন করে না করব! আমার তো একটিই মেয়ে, সমবয়েসি সঙ্গী নেই বাড়িতে। যাক, ঘুরে আসুক। দু-একদিনের মধ্যেই ফিরে আসবে।
রঙ্গলালের মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। এরকম কথা তো ছিল না। ছুটি ফুরোবার সঙ্গে সঙ্গে সে কলকাতা থেকে রিটার্ন করল, আর তুমি নেই, নতুন জামাইবাবুর সঙ্গে আহ্লাদ করতে গিয়েছ!
দুটো দিন অবশ্য এমন কিছু নয়। কোনও রকমে কাটিয়ে দিতেই হবে।
রঙ্গলাল একটা কথা ভেবেই এসেছিল। ফটকটা সে সারিয়ে দেবে। যেভাবে আছে তাতে বড় খারাপ দেখায়। কম্পাউন্ড ওয়ালের ফাঁকফোকরগুলোও মেরামত করাবে ধীরেসুস্থে। আর বাগানটাও পরিষ্কার করিয়ে মালি রাখবে একটা। হপ্তায় দুদিন মালি আসবে। এখানে ভাল গোলাপ হয়। শীত আসছে। দু-চারটে গোলাপ আর মরসুমি ফুল রাখলে মন্দ হয় না।
কিন্তু বাড়ি তো তার নয়। করবে কেন?
“মাসিমা?”
“বলো বাবা।”
“আপনি যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলি?”
“মনে করব কেন?”
“আমাদের অফিসের এক ছুতোর মিস্ত্রি আছে। তাকে বলেছিলাম, এ বাড়ির ফটকটা একটু মেরামত করে দিতে। তার কাছে ঝড়তিপড়তি কাঠ আছে। একটা কি দুটো দিনের ব্যাপার। সে করে দিয়ে যেতে চাইছে। মানে, ফটকটা ঠিক না করলে যখন তখন গোরু-ছাগল কুকুর ঢুকে যায়। সারিয়ে নেওয়াই ভাল।”
“খরচ?”
“ও কিস্যু না। আমাদের অফিসের মিস্ত্রি। অর্ধেক দিন হাত গুটিয়ে বসে থাকে। …আপনি এ নিয়ে ভাববেন না। এ বাড়িতে তো আমিও থাকি।”
“যা ভাল বোঝ করো।”
রঙ্গলাল এখন শুধু ফটক নিয়ে থাকল। একসঙ্গে বেশি লাফাবার চেষ্টা করা উচিত নয়। ড্যামেজ হয়ে যেতে পারে।
পরের দিনই এক ছুতোর মিস্ত্রি ধরে আনল রঙ্গলাল। অফিসের ধারেকাছেও থাকে না।বলল, একদিনে মেরামতি করে দিতে হবে। কাঠের দাম মজুরি আমি দিচ্ছি। তুরান্ত হাত লাগাও।
রাত্রে রঙ্গলাল অতি বিমর্ষ চিত্তে টেপ রেকর্ডারে সেই গজলটা বাজাতে লাগল। ‘ইয়ে জান তুম না লোগে তো ইয়ে আপ জায়েগি…”
বাইরে কার্তিকের আকাশ, কৃষ্ণপক্ষ চলছে। কত তারা আকাশে। হেমন্তের গন্ধ লেগেছে গাছপালায়, কুয়াশা নামা শুরু হল।
ডুমুর নেই। ধ্যুত—কোনও মানে হয়!
তিন দিনের দিন অফিস থেকে ফিরে এসে দেখল, ডুমুর এসে গিয়েছে।
বাঁচা গেল! ‘আনন্দে ভরিল মন, কুসুমসুবাস এল নিশীথ শয়নে…’
সন্ধেবেলায় ডুমুর এল। হাতে চায়ের কাপ, একটা প্লেটে দুটো বালুসাই আর সেউ নিমকি।
“কী, রঙ্গবাবু! কেমন আছেন? কলকাতায় কেমন কাটল?” মজার গলায় বলল, ডুমুর।
“তোমার কেমন কাটল গিরিডিতে?”
“মজাসে। অনেক মজা হল, হই হই। দিনগুলো যে কেমন করে কেটে গেল খেয়াল করতেই পারলাম না।’’
“হাতে ওসব কী?”
“বিজয়া করুন।”
“মাসিমা করিয়েছেন।”
“আরে এ অন্য বিজয়া, এমন বালুসাই খাননি জীবনে। বাইরে থেকে আনা। নিন, খেয়ে নিন।
রঙ্গলাল প্লেটটা নিল। বলল, “আমি ফিরে এসে দেখলাম তুমি নেই—!”
“এই রকমই হয়। আমি ফিরে এসে দেখলাম, বাড়ির ফটকটা সারাই হয়ে গেছে।”
“খারাপ হয়েছে?”
“বলেছি নাকি?”
বালুসাই মুখে দিয়ে রঙ্গলাল বলল, “বাঃ, বেশ তো?”
‘মহাদেব হালুইকরের বালুসাই। গিরিডির নয় মশাই…বাইরে থেকে আনা।”
“ভেরি গুড।…তোমার জন্যে একটা জিনিস এনেছি। সামান্য জিনিস।”
“কী?”
“দাঁড়াও খেয়েনি আগে। সুটকেসে আছে।”
রঙ্গলাল তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করতে লাগল।
ডুমুর দাঁড়িয়ে। পরনে ছাপাশাড়ি, মস্ত বিনুনিটা পিঠের পাশে ঝুলছে। কালো মুখে যেন আলো জ্বলছে খুশির।
“গিরিডিতে গিয়ে তুমি আরও ব্রাইট হয়ে গিয়েছ?” রঙ্গলাল বলল।
“কই! বাজে কথা।”
“রিয়েলি! কী ব্যাপার বলো তো?”
“কিছুই না। খেয়েছি দেখেছি আড্ডা মেরেছি…”
“জলবাতাসের গুণ। মনের ফুর্তি।”
ডুমুর আড়চোখে দেখল রঙ্গলালকে।
খাওয়া শেষ করে চায়ের কাপ তুলে নিল রঙ্গলাল। “আরে, তুমি বসবে না।” “বসছি।” মোড়ায় বসল ডুমুর।
“দাঁড়াও, জিনিসটা বার করি।” মাটিতে কাপ রেখে, সুটকেসটা টেনে বার করল রঙ্গলাল তক্তপোশের তলা থেকে। চাবি লাগানো ছিল না। খানিকটা আগে সিল্কের মাফলারটা বার করেছে রঙ্গলাল। গলায় জড়ানো ছিল। গলাটা আজ বিকেল থেকেই খুসখুস করছিল। হয়তো সিজন চেঞ্জের সঙ্গে।
রঙ্গলাল একটা কৌটো বার করল। গোল কৌটো। বেশ রংচঙে কাগজ মোড়া। কৌটো খুলে দেখাল ডুমুরকে। “এটা আজকাল মার্কেটে খুব চলছে। ফ্যান্সি জিনিস। সিলভার ব্রেসলেট। চুড়িই বলতে পার। প্লেটিং করা আছে। দু-চারটে কুচি লাল পাথর। বাজারে দারুণ ডিম্যান্ড। ফ্যাশানেবল প্রোডাক্ট। মাপটা ঠিক হল কি না কে জানে! আন্দাজে কেনা। নাও ধরো।…দেখো কেমন?”
ডুমুর নিল। দেখল।
“হাত মে লাগাও জি” ঠাট্টার গলায় বলল রঙ্গলাল। “দেখো, ফিট করে কি না?”
ডুমুর হাতে দিল। চুড়িটা তার হাতে মানিয়ে গেল।
চায়ের কাপ মাটি থেকে আগেই তুলে নিয়েছে রঙ্গলাল। চুমুক দিচ্ছিল। খুশি হয়ে বলল, “বিউটিফুল! ফিট করে গেছে! কী হাত।”
“কার।’’
“তোমার, আবার কার?”
“এর দাম কত?”
“দা-ম! যা, এ আবার কী! এসব হল শখের জিনিস, নট ফর সিন্দুক। মেয়েরা শখ করে পরে। বউদিকে দিয়ে পসন্দ করিয়ে নিয়েছি। দাম কিছু না!”
“বউদি?”
“আমার বউদি।”
“ও।”
“আচ্ছা, এবার তোমায় সেই গানটা শোনাই। ওই দেখো টেপ রেকর্ডার, ক্যাসেট।”
ডুমুর দেখল। হয়তো আগেই দেখেছে। কিছু বলেনি।
রঙ্গলাল নাচতে নাচতে গিয়ে ক্যাসেট দেখে টেপ রেকর্ডারে লাগিয়ে দিল।
ক’ মুহুর্ত পরেই গান শোনা গেল : ‘ইয়ে জান তুম না লোগে তো ইয়ে আপ জায়েগি…!’
গানটা ভাল।
শেষও হয়ে গেল এক সময়।
“কী! বলেছিলাম কী!” রঙ্গলাল খুশির গলায় বলল, “আমি বাজে কথা বলি না। ভাল ভালই, তা আমার কাছে তোমার কাছেও।’’
ডুমুর চুপ। আড়চোখ করে কী দেখছিল। ভাবছিল। হঠাৎ বলল, “কিন্তু অন্য একটা মুশকিল হয়ে গিয়েছে…।”
“কী?”
“ওই যে জান বলছেন—ওটা তো নেওয়া যাবে না আর।”
“কেন? কেন?” রঙ্গলাল যেন দু পা এগিয়ে গেল।
ডুমুর একটু চুপ। পিঠের বিনুনি যেন পিঠের কাছে সুড়সুড় করছিল। হাতের ঝাপটায় ঠিক করে নিল। বলল, “হয়ে গেছে।”
“হয়ে গেছে! যাঃ! হাউ হয়ে গেল?”
“ইয়ে—মানে ওই যে এবার গিরিডিতে গেলাম। তা জামাইবাবু একজনের ব্যবস্থা করেছে। বড় মাসিকে বলেছে। বাড়ির সবাইকে। ওদের পছন্দের পাত্র…”
রঙ্গলাল মাথা নাড়তে লাগল। “জামাইবাবুর পছন্দ!…কোথাকার কে…”
“ঝাঁঝায় থাকে।”
“ঝাঁঝাকে যা যা করে দাও। কী নাম?”
“নাম আবার কী? ওই ইয়ে—এমনি নাম—শ্রীবিলাস—”
“ধ্যৎ বি-বিলাস! বিড়ি বিড়ি গন্ধ। করে কি ব্যাটা!”
“জামাইবাবুর মতন রেলে চাকরি।”
“রেলওয়ে ক্লার্ক!”
“আজ্ঞে না। টিটি মিটি। বেড়াবার পাস পায়, ডিউটি নিয়ে বেরুলে দুহাতে…”
“বুঝেছি। শেম! ডুমুর তুমি এইসব হাতকে হাত বলছ। ডোন্ট কল ইট হাত ওগুলো হস্ত…ওদের হস্ত করে সমস্ত কাঙালের ধন চুরি। ঘুষ-ইটার…! প্লিজ !”
“তা আমি কী করব?”
“দেখতে কেমন?”
“চোখে দেখিনি, ফোটো দেখেছি।”
“আরে ফোটো কেউ বিশ্বাস করে। ফোটোতে দিনকে রাত করা যায়, রাতকে দিন। তোমায় ভড়কি মারছে। বিশ্বাস করবে না।…আমাকে তুমি নিজের চোখে দেখছ! কী আমি বাজে দেখতে? পাঁচ ফুট সাড়ে নয় ইঞ্চি, ওজন সাতষট্টি, এম-কম পাস, কাঁটা কারখানার অ্যাসিসটেন্ট অফিসার-ইন-চার্জ, কলকাতার নারকোলডাঙায় বাড়ি, রেসপেক্টেবল ফ্যামিলি আমাদের, বাবা স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিল, ভেরি অনেস্ট ম্যান, বাবা নেই, মা আছে। দাদা বউদি বাচ্চু…। ইউ নো এভরিথিং। কোনও সিক্রেট আমার নেই।
“জামাইবাবু ওই শ্রীবিলাসদের—’’
আবার শ্রীবিলাস! কোনও ভদ্দরলোকের নাম অমন—”
“তোমার নামও তো রঙ্গলাল” ডুমুর এবার তুমিই বলল।
“রঙ্গলাল একটা ক্ল্যাসিক নাম। সেই বিখ্যাত রঙ্গলাল বাঁড়ুজ্যের—কথা ভাব। স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে..রিমেমবার! সেই রঙ্গলাল আর আমি—! তুমি ভাই প্লিজ ঝাঁঝার শ্রীবিলাস বোষ্টমকে কাটিয়ে দাও। ও তোমার চয়েস নয়, আমিই রাইট চয়েস। রাইট চয়েস বেবি!” রঙ্গলাল ঝুঁকে পড়ল।
ডুমুর হঠাৎ বলল, “ওমা, ঠিক তো! ওরা বোস্টম নয়, তবে ও নিরামিষাশী। কী ভাল! আমার আবার নিরামিষ বলেই বেশি পছন্দ।
“ছাগল!”
“কী?
“না। কিছু না!” রঙ্গলাল সরে এল। “যাক গে, তোমার কথাটা তা হলে কী দাঁড়াচ্ছে! তুমি আমার প্রপোজাল অ্যাকসেপ্ট করছ না? বিয়ে করতে রাজি নও!”
“বিয়ে! পুরুত ডেকে?”
“সই করেও হতে পারে।”
“যেভাবেই হোক, সেই বাসরঘর, ফুলশয্যে! ছি !”
রঙ্গলাল অবাক। “ফুলশয্যে কী দোষ করল! সবাই করে। সোশাল প্র্যাকটিস।”
“না বাবা, ওই এক বিছানায় শোয়া। তোমার সঙ্গে…। আমি পারব না। ন্যাকা ন্যাকা কথাই বা কী বলব!”
“ঝাঁঝার বেলায় কী হত? সে তোমায় কোন শয্যায় শোয়াত?”
ডুমুর আড়চোখে দেখল রঙ্গলালকে। বলল, “বারে, তাকে আমি চিনি? সে কী করত, কী করবে—কেমন করে বলব!”
রঙ্গলাল এবার অধৈর্য হয়ে পড়ল। বলল, “ও কে। চ্যাপ্টার ক্লোজড। আমি জানি, দিল হি তো হ্যায় ন সঙো-যিশু দর্দ সে ভর্ন্ আয়ে কিউ? রোয়েঙ্গা হম হাজারো বার, কোঈ হমে সতায়ে কিউ!…আমার এই হৃদয়, হৃদয়ই, ইট বা পাথর নয় যে দুঃখে ব্যথা পাবে না। যদি কেউ এই হৃদয়কে আঘাত করে তা হলে আমি না কেঁদে কেমন করে থাকি।…ও কে ডুমুর, গুড বাই…”
ডুমুর চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে রঙ্গলালকে দেখছিল। দেখতে দেখতে বলল, “একটা টাকা দাও তো?”
“টাকা!” রঙ্গলাল থতমত খেয়ে গেল। “টাকা কী করবে?”
“দাও না। কয়েন দেবে।’’
রঙ্গলাল আলনায় ঝোলানো জামা হাতড়ে একটা গোল টাকা বার করে ডুমুরকে দিল।
টাকা নিয়ে ডুমুর বলল, “শোনো, এটাই ফাইন্যাল। টাকাটা টস করব। হেড টেল। যদি তুমি ঠিক ঠিক বলতে পার, ঝাঁঝা বাদ ; যদি না বলতে পার তুমি বাদ! বুঝলে?”
রঙ্গলাল ঘাবড়ে গেল! এ আবার কী? কোন দরের ‘হ্যাঁ’ ‘না’ ঠিক করা! টস করে বিয়ের পাত্র বাছাই। রঙ্গলাল বলল, “কী পাগলামি করছ? কয়েন টস করে এসব সিলেকশান হয়?”
“হয়! বিয়ে মানেই তো তাই! লাগলে তুক, না লাগলে তাক! সবই কপাল।..তুমি টাকা ছুড়বে, না, আমি! কে হেড টেল বলবে? তুমি বলবে!”
রঙ্গলাল ভয় পেয়ে গেল। সর্বনাশ! কল তো ভুল হতেই পারে! ক্রিকেট খেলায় এসব চলে! জীবনের খেলায় চলে না। ডুমুর সত্যিই পাগল। রঙ্গলালের ভয় করতে লাগল। যদি ভুল হয়? হতেই পারে!
“কী আমি টাকা ছুড়ব। না তুমি ছুড়বে! ডাকবে কিন্তু তুমি।”
রঙ্গলালের গলা বন্ধ হয়ে এল। “তুমিই ছোড়। তবে এটা ফেয়ার হল না ডুমুর।”
ডুমুর টাকা ছুড়ল। উঁচুতে উঠে ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে পড়ার সময় রঙ্গলাল চোখ বন্ধ করে ডাক দিল, ‘হেড’।
ঠক করে মাটিতে পড়ল টাকাটা।
ডুমুর বলল, “কে দেখবে? তুমি না আমি?”
“তুমিই দেখো,” রঙ্গলালের গলা শুকিয়ে গেছে।
ডুমুর টাকার কাছে গিয়ে মাটিতে বসল। দেখল। তারপর উঠে দাঁড়াল। টাকা তুলল না। খুব আক্ষেপের গলা করে বলল, “তোমার কপাল খারাপ। হেরে গেলে! কী করবে বলো! দুঃখ করো না। জীবনে কত হারজিত আছে!” বলে একটু হাসল। “আমি যাই। রাত হয়ে যাচ্ছে।”
বালুসাইয়ের প্লেট আর চায়ের কাপ তুলে নিয়ে ডুমুর চলে যেতে যেতে বলল, “মন খারাপ কোরো না।…আমি তো কিসের ছাইপাঁশ! তুমি কত সোনাদানা পেয়ে যাবে। অত ভাল ছেলে! চলি।”
ডুমুর চলে গেল।
রঙ্গলাল এতটা ভাবেনি। তার মাথায় যেন ছাদ ভেঙে পড়েছে। বেচারি এখন কী করবে! মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছিল! শালা, একটা ডাকও ঠিক মতন দিতে পারল না। বোগাস।
ঘরের মধ্যে বার কয়েক পায়চারি করল রঙ্গলাল। এ-বাড়িতে আর থাকা চলবে না। থাকলে তুষের আগুনে পুড়ে মরতে হবে। হাম ভি বনে হি রিন্দ…। আমি মদ্যপান করার জন্যে মেতে উঠেছিলাম, জানতাম না শূন্য পাত্র হাতে ফিরে আসতে হবে।…
রঙ্গলাল প্রায় কেঁদেই ফেলেছিল। ইচ্ছে হল, মাটিতে পড়ে থাকা টাকাটা লাথি মেরে সরিয়ে দেয়। শালা, নেমকহারাম, চিট। তুই আমার পকেটের টাকা হয়ে আমায় ঠকালি!
লাথি মারতে গিয়েও লাথি মারা হল না। পিঠ নুইয়ে তুলে নিতে গেল টাকাটা। নিতে গিয়ে অবাক। চোখকে কেন বিশ্বাস করতে পারছিল না। আরে শালা, এ কী! এ তো হেড। রঙ্গলাল ঠিক ডাকই দিয়েছিল। ডুমুর তাকে মিথ্যে বলল? কেন? তার কি চোখের ভুল হয়েছিল! নাকি মজা করে গেল। ইচ্ছে করেই শয়তানি করলে! দারুণ বিচ্ছু তো!
এখন কী করবে রঙ্গলাল? ডাকবে ডুমুরকে। ডুমুর যদি বলে, মশাই—চালাকি রাখো। আমি থাকতে থাকতে কেন দেখলে না! আমার সামনে? এখন টেলকে হেড করে রেখে আমায় দেখাতে ডাকছ। চালাকি!
ডুমুর তা বলতে পারে। বলা সম্ভব! অথচ ভগবানের দিব্যি, রঙ্গলাল ওই টাকা স্পর্শ করেনি।
সারা রাত তো এভাবে থাকা যাবে না। ছটফট করতে করতে মরে যাবে রঙ্গলাল। সে ভদ্রসন্তান, চিট নয়।
কেমন খেপার মতন রঙ্গলাল বারান্দায় বেরিয়ে এল।
বেশ কুয়াশা জমছে। হিম পড়ছে। তারাগুলো ঝাপসা।
“ডুমুর! ডুমুর! এই ডুমুর?”
বার কয়েক হাঁক দেবার পর ডুমুর বারান্দার ওপারে জাফরির কাছে এল।
“কী হয়েছে? চেঁচাচ্ছ কেন?”
“তুমি আমায় ব্লাফ মারলে! আশ্চর্য! হেডকে টেল বলে ঠকিয়ে এলে! আমি স্পষ্ট দেখছি হেড। মাই কল ওয়াজ রাইট।”
ডুমুর একটু চুপ করে থেকে বলল, “তো কী হয়েছে! তুমি দয়া করে একটু ঘাড় নুইয়ে দেখলেই পারতে! লাটের মতন দাঁড়িয়ে থাকলে কেন?”
“আমি তোমায় বিশ্বাস করেছিলাম।”
“এখন?”
“এখনও করছি। তুমি আমাকে নিয়ে নাচাচ্ছিলে!”
“আহা! …কত রঙ্গ জানো জাদু, কত রঙ্গ জানো! …দড়ি দিয়ে না বাঁধতেই যে এত নাচে, পরে সে কত নাচবে!…এখন ঘরে যাও! মা ডাকছে। কাল কথা হবে।”
“পাকা কথা।” বলে রঙ্গলাল প্রাণের সুখে হাসতে লাগল।
রত্নলাভ
গল্পটা রত্নদিদির মুখেই শোনা। তাঁর গল্প।
গল্প শুরুর আগে একটু ভূমিকা সেরে নিতে হয়। আমাদের এক আত্মীয়ার বিয়েতে গিয়েছিলাম ধানবাদের দিকে। কোলিয়ারিতে। না গিয়ে উপায় ছিল না, আত্মীয়জনে দুঃখ পেতেন, ক্ষুব্ধ হতেন। বিয়ে বাড়িতে গিয়ে দেখি, স্বজনে কুটুমে বাড়ি একেবারে হট্টশালা। চেনাজানা প্রায় সকলেই এসেছেন। এমন কি রত্নদিদিও। ওঁকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। বয়েস সত্তর ছাড়িয়েছে, থাকেন হাজার মাইল তফাতে, অন্তত দু জায়গায় ট্রেন বদল করে আসতে হয় এদিকে, তবু এসেছেন।
অনেককাল পরে রত্নদিদিকে দেখলাম। বছর পনেরো তো অবশ্যই। বললাম, “তুমি একলা এসেছ! এলে কেমন করে? বয়েস তো হয়েছে, দিদি। ছেলে তোমায় ছাড়ল?”
রত্নদিদি বললেন, “আসব না কেন? ছেলে বউ কি ছাড়তে চায়। ঝগড়া মাচিয়ে দিলুম। নাতি বলল, এ বুঢড্ডি রেল ডিব্বায় তুমি উঠতে পারবে না, পুলিশ পাকড়াও করবে। বললাম, যা যা আমায় পুলিশ দেখাস না, তোর বাপের মতন পুলিশ আমি ট্যাঁকে খুঁজি।”
রত্নদিদির কথা শুনে হেসে ফেললাম।
“পারল আটকাতে! কেমন গটগটিয়ে চলে এলাম। নাগপুর পর্যন্ত একটা লোক সঙ্গে ছিল। তারপর একলা।”
“তোমার সাহস আছে।”
“থাকবে না কেন! আমি কি তোদের মতন ভেতো? এই দেখ, এখনও আমার যোলোটা দাঁত আছে নিজের, চোখে চশমা পরি সেলাই-ফোঁড়াইয়ের সময়, নয়ত আকাশের চিলও দেখতে পাই। কান আমার ঠিক আছে। তবে কি জানিস ভাই, ডান হাতের কনুইটা মাঝে মাঝে খটাস করে আটকে যায়। ভাঙা জিনিস মেরামত হলে কলকবজায় একটু গোলমাল থাকেই। কী করব বল? ভগবানের তো কামারের হাত, দু-চারটে হাতুড়ির ঘা না মেরে কি রেহাই দেয়!”
বয়েসে মানুষের অনেক কিছুই বদলে যায়, তবে গড়ন বিশেষ বদলায় না। দিদি মাথায় লম্বা ছিলেন, দোহারা গড়ন। সেই রকমই আছেন প্রায়। পিঠ হয়ত সামান্য নুয়ে পড়েছে, কৃশ হয়েছেন কিছুটা। গাল ভেঙে মুখ সরু সরু দেখায়। মাথার সব চুল সাদা ধবধবে। ঘাড় পর্যন্ত চুল। মাথার কাপড় দেন না। গায়ের রং তামাটে, ঝকঝকে ভাবটা আর নেই। রত্নদিদিকে দেখলে বেশ বোঝা যায়, বাইরের জল বাতাস ধুলো ময়লার শুধু নয় সেখানকার মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশারও একটা ছাপ পড়ে গিয়েছে হাবেভাবে চেহারায়। ওঁর নিজের কথাবার্তায় ততটা হয়ত পড়েনি। দিদি বিধবা, কিন্তু থান পরেন না, পরেন মিলের সাদা জমির মিহি সুতোর শাড়ি, কালো বা খয়েরি ধরনের ছাপা পাড় থাকে শাড়িতে। গলায় একটি সরু হার, হাতে দু গাছা ফিনফিনে চুড়ি। কানে কিছু পরেন না, আঙুলেও আংটি নেই।
রত্নদিদি আমাদের সামান্য দূর সম্পর্কের দিদি। তাঁকে যে বেশি দেখেছি তাও নয়, তবু আগে জামাইবাবু বেঁচে থাকতে ওঁরা দু-চার বছর অন্তর একবার করে বাপ শ্বশুরের দেশে আত্মীয়স্বজনের কাছে বেড়াতে আসতেন, দেখাশোনা করে যেতেন যতটা পারতেন আমাদের সঙ্গে। জামাইবাবু চলে যাবার পর সে পাট চুকে গিয়েছে।
অনেককাল পরে আবার রত্নদিদিকে দেখে ভালই লাগল। তাঁর যেমন বয়েস হয়েছে, আমাদেরও তেমন কম বয়েস হল না। আমি নিজেই তো কবে ষাট ছাড়িয়ে গিয়েছি।
কথায় কথায় একবার বললাম, “দিদি, হাজার মাইল ঠেঙিয়ে যখন এদিকে এসেই পড়েছ, তখন বিয়ের পাট চুকলে আমাদের সঙ্গে কলকাতায় চলো। দশ বিশ দিন থেকে সকলের সঙ্গে দেখা করে ফিরে যেও। তোমার কোনো অসুবিধে হবে না। তোমাকে ফেরত পাঠানোর দায়িত্ব আমাদের।”
রত্নদিদি হেসে বললেন, “না ভাই, আমায় আর টেনে নিয়ে যাস না। পাক্কা দশ দিনের ছুটি মঞ্জুর করেছে ওপরঅলা। মাথার ওপর এখন বড় ছেলে, বুঝলি তো! এ হল অন্য রাজার রাজত্ব। হুকুম না মানলেই পেয়াদা পাঠাবে। …না রে, এবারে হল না, আবার যদি কোনোদিন আসি তখন কথা রাখব তোদের। এবারও কি এমনি এলাম ভাবছিস! দেখলাম, আমাদের ডালপালায় এটি হল শেষ শুভকাজ। না এলে হয় না। তা ছাড়া আমাদের বাঙালি বাড়ির বিয়ে-থা কতকাল দেখিনি। দেখতে সাধ হল।”
“কেমন দেখলে?”
“ভাল লাগল না। এ কি বিয়ে রে! এ যেন সত্যনারায়ণের পুজো। নৈবিদ্যি সাজিয়ে বসে থাকলি তোরা আর একটা তোতলা বামুন এসে দুটো মন্তর পড়ে চলে গেল। তারপর তো দেখি যা হচ্ছে সবই ভাড়ার ব্যাপার। ভাড়ার লোক বাসর সাজায়, ভাড়াটে একদল লোক এসে রান্নবান্না করে খাইয়ে যায়, কতক লালসবুজ বাতি জ্বাললি তোরা, ঝম্পঝম্প বাজনা বাজালি— ব্যাস, বিয়ের পাট চুকে গেল। এই বিয়ে দেখে কি সাধ মেটে নরেন! বিয়ে ছিল আমাদের সময়ে। বিয়ে তো সাত পাকে মাত্তর, কিন্তু বিয়ের আগে পরে ঊনপঞ্চাশ পাক! কত হইচই, হাসিখুশি, হইহুল্লোড়, মেয়েদের আচার, ভোজের ভিয়েন, বিয়েতলা সাজানো, পিঁড়ি পাতা, আলপনা— বিয়ের রুমাল পদ্য, বাসরের রঙ্গতামাসা… কোথায় গেল সেসব! যাই বলিস, আমার বাপু মন ভরল না।”
“আজকাল এই রকমই হয়, দিদি ; মানুষের আর সময় কোথায়? লোকবল অর্থবল— তাই বা কোথায়?”
“তা নয় রে, ভাই, এখনকার দিনে সবাই কাঁচা রঙে কাজ সারতে চায়, পাকা রঙের দিন ফুরিয়েছে।”
এমন সময় সত্যদার গিন্নি কৃষ্ণাবউদি বলল, “দিদি, এই বিয়ে নিয়ে টানা-হেঁচড়া হচ্ছিল। মেয়ের নিজের পছন্দ, ছেলেরও। চেনাজানা হয়েছিল ওদের। আমাদের তো মেয়ের তরফ, বিয়েটা ভালোয় ভালোয় চুকে গেছে, এতেই আমরা খুশি।”
কথাটা বোধ হয় জানা ছিল না রত্নদিদির। শুনলেন। তার পর কী মনে করে যেন হাসলেন। বললেন, “চেনা-জানা বিয়ে! তাই নিয়ে টানা-হেঁচড়া। আমায় আর ওসব বলিস না। আমার বিয়ের গল্প জানিস! কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ শেষ হতে লেগেছিল আঠারো দিন। আমার বিয়ে নিয়ে, আঠারো মাসের লড়াই! সে যে কী কাণ্ডই হয়েছিল তোরা ভাবতেই পারবি না।”
গল্পটা সত্যি আমাদের জানা ছিল না। জানার কথাও নয়। একসঙ্গে তো মানুষ নয়, একেবারে নিজেরও কেউ নয় রত্নদিদি। ওঁরা থাকতেন এক প্রান্তে আমরা অন্য প্রান্তে, আর রত্নদিদি? বিয়ের সময় আমাদের নিশ্চয় শিশু অবস্থা।
আমি হেসে বললাম, “তোমার বিয়ের গল্পটাই না হয় বলো, শুনি।”
“শুনবি! তা হলে বলি?”
না-শোনার কারণ ছিল না। বিয়েবাড়ি এখন অনেকটাই নিঝুম। বিকেলের গোড়ায় কন্যা-বিদায়পর্ব মিটে গিয়েছে। দেখতে দেখতে সন্ধে হয়ে এসেছিল। বাতি জ্বলছে ঘরে। বাইরে প্রথম ফাল্গুনের মরা শীত আর সদ্য বসন্তের দু-চার ঝলক বাতাস মেশামিশি হয়ে আছে। বাড়িটার চেহারা উড়ুখুড়ু, খানিকটা ম্লান। ছেলেছোকরার দল যে যেখানে পেরেছে শুয়ে পড়ে আরাম করে নিচ্ছে আজকের মতন। কাল থেকে আবার তত্ত্বতাবাসের খাটুনি।
আমাদের দিকের অন্য ব্যবস্থা। বয়স্কজন থাকব বলে যথাসম্ভব সুখসুবিধের ওপর নজর রাখা হয়েছিল।
রত্নদিদির ঘরটি ছোট। খাট বিছানা পাতা। সেখানে বসেই আমরা চার-পাঁচজনে গল্পগুজব করছিলাম।
দুই
রত্নদিদি তাঁর গল্প শুরু করলেন।
“একটু গোড়া থেকেই বলি, না বললে বুঝবি না,” রত্নদিদি বললেন। “আমার বাবা ছিল পোস্ট মাস্টার। সরকারি চাকরি। চাকরির লেজ যত বাড়ে বাবাও তত পুরনো হয়, আর দু-তিন বছর অন্তর বদলি পায়। ছোটখাটো শহরেই বদলি হত বাবা। আমরাও বাবার পেছনে পেছনে আজ মতিপুর, কাল গজুডি, পরশু রামনগর ঘুরে বেড়াই। পাঁচ ঘাটের জল খাই পাঁচ জনে। পাঁচ জন বলতে বাবা মা আমি আমার ছোট ভাই অনু আর আমাদের এক পুষ্যি ভরতদাদা। ভরতদাদা বাবার কাছেই দশ-বারোটা বছর থেকে গিয়েছিল। বাড়ির হাটবাজার করা থেকে পাঁচ-মেশালি ফাইফরমাশ খাটা ছিল ভরতদাদার কাজ।
“আমার বাবাকে লোকে বলত, মাস্টারবাবু, কেউ বা বলত মাস্টারমশাই। নিজের কাজকর্মে বাবার সুনাম ছিল, খাতিরও করত লোকে। বাবার ছিল দুটো শখ। তাস খেলাটা অবশ্য শখ ছিল না, ছিল নেশা ; শখ বলতে এই জ্যোতিষীবিদ্যে করে বেড়ানো, আর মাঝে মাঝে এস্রাজ টেনে নিয়ে বসে নিজের মনে একটা সুরটুর বাজানো। বাবার আর-একটা ঝোঁক ছিল, সিদ্ধি খাবার। সিদ্ধির সরবত, সিদ্ধির গুলি— এ বাবা প্রায়ই খেত, নিজের হাতে তরিবত করে তৈরি করেই খেত।
“মা ছিল আমার নির্বিবাদ মানুষ। শান্তশিষ্ট। হাসিখুশি। দোষের মধ্যে মা গাদা গাদা পান খেত। আবার কত কী, বাবার আনা কাঁচা সিদ্ধিপাতাও মাঝে মাঝে পানের মধ্যে মিশিয়ে দিব্যি খেয়ে নিত। বলত এতে মুখশুদ্ধি হয়।
“তা এইভাবে বড় হতে হতে আমার বয়েস হয়ে গেল পনেরো। শাড়ি পরতে শুরু করেছি। আমি মাথায় ঢেঙা, গায়ে হিলহিলে, লম্বা লম্বা হাত-পা। ওপর পাটির ডান দিকের দাঁতে এক গজদন্ত। জোরে হাসলে দাঁতের ছটা বেরিয়ে যায়।
“আমরা তখন বরিহাগঞ্জ বলে একটা ছোট শহরে থাকি। কে একজন—এখন আর মনে পড়ে না, আমার এক বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এল। আমাদের সময় পনেরো ষোলোয় আকছার বিয়ে হত। তা ছাড়া সম্বন্ধ আনলেই তো বিয়ে হবে না, কথাবার্তা চলতে চলতে, দেখাশোনা, পছন্দ— সেসব করতে করতে কম করেও একটা বছর। ওরই ফাঁকে মেয়ের বয়েসও বেড়ে যায়।..তা প্রথম সম্বন্ধটা দুটো ধাপ এগুতে পারেনি। কেঁচে গেল। কিন্তু ওই যেমন রেল স্টেশনে দেখেছিস না গাড়ি আসছে জানাবার আগে ঢংঢং ঘণ্টা বাজে, এটাও সেরকম। সম্বন্ধ একবার শুরু হওয়ার মানে জানান দেওয়া হয়ে গেল, মেয়ে এবার তোমার বিয়ের ঘন্টি বেজে উঠেছে।
“প্রথমটার কথা আমার মনে নেই। কোথাকার ছেলে কে জানে, পাতে দেবার যুগ্যি নিশ্চয় ছিল না, নয়ত মা বাবার গরজই হল না কেন! তা সে যাই হোক, তখন থেকেই মাঝে মাঝে কথা ওঠে, এক আধটা চিঠিপত্তরও আসে। ষোলো পেরিয়ে আমি যখন সতেরোয় পা দিয়েছি, তখন একটা সম্বন্ধ এল জামালপুর থেকে। কথাবার্তাও দু-চার ধাপ এগুল। শেষে ভেস্তে গেল। বাঁচা গেল।
“সেই বছরেই শেষাশেষি একটা ছোঁড়াকে একদিন আমাদের বাড়ির কাছাকাছি দেখলুম। পোস্ট অফিস আর ইউনিয়ন বোর্ডের ছোট হাসপাতালের কাছেই ছিল আমাদের থাকার বাড়ি। ছোট বাড়ি, মাথায় টালির ছাদ, সামনে খুঁটি পুঁতে বেড়া দিয়ে বাগান করেছি আমরা, সামনে উঁচু-নিচু মাঠ, আম আর কাঁঠালের বড় বড় গাছ দু-চারটে, ও পাশে হাসপাতাল। বাড়ির গায়েই আমাদের ইদারা। সে-জলের স্বাদই আলাদা।
“প্রথমে বুঝিনি ছোঁড়াটা কোথথেকে এল? পরে শুনলাম, হাসপাতালের নতুন ডাক্তারবাবুর ভাগ্নে। মামা-মামির বাড়িতে এসেছে। তা তার মামার বাড়িতে এসেছে আসুক, আদর খাক মামির, আমার তাতে কী! কিন্তু ছোঁড়াটার ভাব-গতিক তো ভাল নয়। মালকোঁচা মেরে ধুতি পরা, গায়ে হাফ শার্ট, পায়ে কাবলি স্যান্ডেল। তখন প্যান্ট পরার চলন হয়নি এত, ধুতিই পরত লোকে। ছেলেটার বয়েস বেশি নয়, আমার চেয়ে বড়, তবে অনেক বড় নয়, বাইশ-টাইশ হবে। ডাক্তারকাকার সাইকেল নিয়ে হাসপাতালের মাঠে আমাদের বাড়ির সামনে সকাল বিকেল চক্কর মারে। আর আমায় দেখলেই, সাইকেল নিয়ে কসরত দেখায়। হাসে। চোখ নাচায়।
“ডাক্তারকাকার মেয়ে মানি ছিল আমার ন্যাওটা। বছর বারো বয়েস। দিদি বলত আমায়। আমার কাছে পড়তে আসত মাঝে মাঝে, সেলাই শিখত ; বাজার কি স্টেশনের দিকে দরকারে যেতে হলে মানি আমার সঙ্গে থাকত।
“মানিকে জিজ্ঞেস করলাম, তোর ওই দাদাটার নাম কিরে? মানি বলল, ডাকনাম লাল। ভাল নাম লালমোহন। …নামটা বলেই ফেললাম। আমার অত লজ্জা নেই। মানামানিও নেই।
“নাম শুনে হাসি পেল। লালুর চেহারায় কোথায় যে লাল ছিল বুঝলাম না। গায়ের রং আমার চেয়েও কালো। গায়ে কাঠ। মুখচোখ চলনসই, বড় বড় চোখ, মাথার চুল ভেড়ার লোমের মতন কোঁকড়ানো।
“মানিকে বললাম, করে কী তোর দাদা? মানি বলল, ডাক্তারি পড়ে। এবার ডাক্তার হবে। আমার তো গোড়ায় বিশ্বাস হয়নি। ওই লালমোহন, অমন হ্যাংলা প্যাংলা চেহারা যার, ফাজিল ফক্কর ধরনের হাবভাব— সেই ছেলে পড়বে ডাক্তারি! মানুষ তো দূরে থাক ওকে ঘোড়ার ডাক্তারি পড়তেও কেউ নেবে না।”
রত্নাদিদি নাকমুখ কুঁচকে ঠোঁট উল্টে এমনভাবে বললেন কথাটা যে আমরা হেসে ফেললাম।
জানলার গায়ে জলের জগ ছিল। কয়েক ঢোঁক জল খেলেন রত্নদিদি। মশলার কৌটো থেকে মশলা বার করে মুখে দিলেন। এ তাঁর নিজের হাতে তৈরি মশলা। জোয়ান মউরি আর কী কী সব মিশিয়ে করা।
“খাবি মশলা?”
আমরা কেউ কেউ মশলা নিয়ে মুখে দিলাম।
“তারপর?”
“তারপর—” রত্নদিদি বললেন, “তারপর দেখি, কথাটা ঠিকই। লালমোহন বাঁকড়োর মেডিকেল স্কুলে ডাক্তারি পড়ে। পড়া প্রায় শেষ করে এনেছে। আমরা যেখানে থাকতাম সেখান থেকে বাঁকড়ো দূরও নয়, ভাগা আদরা লাইন দিয়ে যেতে হয়। …তা একদিন লালুচাঁদ তার মামি আর বোনের সঙ্গে আমাদের বাড়ি বেড়াতে এল। ডাক্তার কাকিমা তো প্রায়ই মায়ের সঙ্গে গল্পগুজব করতে আসত। আমার ছোট ভাইটা তখন হামজ্বর নিয়ে পড়ে আছে। দেখতে এসেছিল ডাক্তার কাকিমা, সঙ্গে লালুচাঁদ। চলে যাবার সময় লালু আমার মাকে বলল, মাসিমা— এই মেয়েটার পেটে কৃমি আছে নাকি? বড় কৃমি থাকলে এই রকম রোগাটে চেহারা হয়। ..মা বলল কই না তো! ও বরাবরই এই রকম। ছিপছিপে তবে কাজেকর্মে তরতরে। লালুচাঁদ হাসল। বলল, বড় কৃমি থাকলে ওই রকম তরতরে হয়। ভেতরে কামড়ায় তো, তাই। আমি কিছু বললাম না তখনকার মতন।
“পরের দিন বিকেল বেলায় দেখি, কাঁঠালতলার একপাশে আড়ালে দাঁড়িয়ে লালু সিগারেট ফুঁকছে। গিয়ে ধরলুম তাকে। চমকে উঠেছিল। বললাম, অ্যাই— কৃমি কত বড় হয়? …আচমকা ধরা পড়লে চোরের যেমন অবস্থা হয় সেই রকম অবস্থা হল লালমোহনের। তোতলাতে তোতলাতে বলল— কেন, বড় বড়ও হয়, এক বিঘত দেড় বিঘত। অনেক সময় জোড়া কৃমিও থাকে। ভেরি ব্যাড। কৃমি মুখ পর্যন্ত উঠে আসে। …বললাম, ও—তা তোমার নিজের পেটে কী আছে, কৃমি না কেঁচো? ছাগলদের পেটে একরকম কেঁচো থাকে লম্বাই আধ হাত।
“লালমোহন থতমত খেয়ে গেল। বলল, তুমি আমায় ছাগল বললে? জানো আমি এল এম এফ পরীক্ষা দিচ্ছি। আজ বাদে কাল ডাক্তার হব।
“ঠোঁট উল্টে আমি বললাম, অমন লম্ফ আর হেরিক্যান ডাক্তার গণ্ডায় গণ্ডায় হয়। … আমার পেটে কী আছে তুমি জানলে কেমন করে? তোমার নিজের পেটের খবরটা নাও আগে গিয়ে। খবরদার, আমার সঙ্গে ফক্কুরি করতে এসো না, তোমার ডাক্তারি ঘুচিয়ে দেব, আমায় তুমি চেনো না।
“বললাম বটে, কিন্তু কাকে! কী কানকাটা নাককাটা ছেলে রে ভাই। মান অপমান জ্ঞান নেই। ধমক খেয়ে তার মজা যেন বেড়ে গেল। সাইকেলের চক্কর শুরু হল একেবারে আমাদের বাড়ির গায়ে। ঘন ঘন দেখতে আসতে লাগল আমার ভাইকে। একটু আড়াল পেলেই আমায় দেখে পিটপিট করে হাসত, আর বলত, শাক দিয়ে কি মাছ ঢাকা যায়, চোখ পাকালে পেটের কৃমি মরে না।
“ভাই সেরে উঠতে না-উঠতে আমি পড়লাম। বড় বয়েসের হাম। সে কী কষ্ট। ডাক্তার লালমোহন আমায় হামে পড়তে দেখল। ততদিনে তার স্কুল খুলে গিয়েছে। চলে গেল।
“ভাবলাম, বাঁচা গেল। আর তো পেছনে লাগতে আসবে না সে!…ওমা, তোরা শুনলে অবাক হয়ে যাবি, লালমোহনের কত বড় দুঃসাহস আর শয়তানি বিদ্যে! আমি সেরে উঠেছি, হঠাৎ একদিন এক চিঠি। একেবারে খামে। ভেবে দেখ কাণ্ডখানা! তখনকার দিনে কোনো গেরস্থবাড়ির আইবুড়ো মেয়ের নামে কি কেউ চিঠি লিখত? আবার খামের ওপরে আমার নাম, নীচে কেয়ার অফ বাবার নাম। ধর, বাবার নাম যদি নাও থাকত— তবু তো পোস্ট মাস্টার। তার মেয়েকে তুমি চিঠি লিখলে সে চিঠি কার নজরে পড়বে গো! বাবার হাতেই পড়ল চিঠি। মায়ের হাত ঘুরে সে চিঠি এল আবার আমার হাতে। ভয়ে লজ্জায় মরি। রাগে মাথায় আগুন জ্বলে যায়। এমন বেহায়া, অসভ্য, হদ্দ বোকা কেউ হয় নাকি? চিঠির খাম আগেই খোলা ছিল। ভেতরে কী দেখলাম জানিস? শুনলে তোদের বিশ্বাস হবে না। চার-ছ লাইনের এক চিঠি লিখেছে লালমোহন। চিঠির ঠিক ঠিক ভাষা আমার মনে নেই, তবে লেখার ঢংটা ওই রকম : ভাই রতনমণি, আসিবার সময় তোমার হামজ্বর দেখিয়া আসিয়াছি। এতদিনে নিশ্চয় তোমার জ্বরজ্বালা সারিয়াছে। বড় বয়সে হামজ্বর অতি মন্দ। পরে বড় ভোগায়। সাবধানে থাকিবে। তোমার কথা মতন আমাদের এখানকার এক নার্শারির কাগজ পাঠাইলাম। ফলফুলের নাম ও দাম পাইবে। সবই লেখা আছে। পয়লা নম্বরের গাছগুলিতে টিক মারা আছে। লক্ষ করিয়া দেখিও। মামাবাবু মামিমাকে আমার প্রণাম জানাইলাম। তোমরা স্নেহ জানিবে। ইতি তোমার লালুদা।
“চিঠি পড়ে আমি আকাশ থেকে পড়ি রে? এক ফালি চিঠি তো চারপাতা ছাপানো নার্শারির কাগজ। ফলফুলের নাম। দাম। আমি একবারের জন্যেও লালমোহনকে ফলফুল নার্শারির কথা বলিনি। আমাদের বাড়ির সামনে তিন হাতের বাগানে একটা কলাগাছ, লাউমাচা একটা। দুটো লঙ্কাগাছ আর ফুলের মধ্যে জবা, চাঁপা আর শীতের সময় দু-চারটে গাঁদা। বাগানে আমার জল দেওয়াও হয় না, ভরতদা দেয়।…আমার মাথায় কিছু ঢুকল না। নার্শারির ছাপা কাগজ কেন পাঠাল লালমোহন? তার মতলবটা কী? ছাপা কাগজগুলো বারবার দেখেও আমার বাপু বিদ্যে হল না বুঝি ওর মধ্যে কী হেঁয়ালি আছে।
রত্নদিদি একটু থামতেই, আমি হেসে বললাম, “হেঁয়ালি ছিল নাকি?”
কৃষ্ণাবউদিও হেসে বলল, “পায়ে ধরে পিসি সাড়া দেয় না মাসি— সেই রকম হেঁয়ালি নাকি?”
রত্নদিদি কাপড়ের আঁচল মুঠো করে মুখের সামনে তুলে জোরে জোরে হাঁচলেন বার দুই। খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। কাল ছিল ত্রয়োদশী, আজ চতুর্দশী। শুক্লপক্ষ। জ্যোৎস্নার বান ডেকেছে যেন বাইরে, বাতাস বইছে।
“ছিল। কিন্তু তখন বুঝিনি”, রত্নদিদি বললেন, “পরে বুঝলাম। নার্শারির ছাপা কাগজ পাঠিয়ে ও বাবা-মায়ের চোখে ধুলো দিয়েছে— সেটা ধরতে পারলেও বুঝতে পারিনি ফলফুলের ছাপা নামগুলোর তলায় যেখানে যেখানে পেনসিলের টিক আছে— সেই অক্ষরগুলো বেছে বেছে সাজিয়ে নিলে বোঝা যায় লালু আমার ‘লাবে’ পড়েছে।”
কৃষ্ণাবউদি জোরে হেসে ফেলে বলল, “আপনি তো বললেন, হেঁয়ালি ধরতে পারেননি।”
“পারিনি তো! কেমন করে পারব।… তারপর লালমোহন আবার যখন এল, আমায় বলল, তোমার মাথায় ঘিলু আছে না গোবর! কিস্যু বুঝতে পারো না। নিয়ে এসো নার্শারির কাগজ বুঝিয়ে দিচ্ছি। গোলাপের ‘লা’ আর বেলের ‘বে নিলে কী হয়— বুঝতে পারো না? ঘেন্টু কোথাকার! …বললাম, সে-কাগজ ফেলে দিয়েছি।…হাঁ হয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, ফেলে দিয়েছ। তুমি মেয়ে, না হান্টারওয়ালি! এই ভাবে কেউ চাবুক মারে বুকে!”
আমরা হেসে ফেললাম। হো হো করে।
সত্যদা বলল, “লালমোহন কি প্রায়ই আসত তোমাদের ওখানে?”
রত্নদিদি বললেন, “আসত মানে! এই তোমার গরমে আসছে, পুজোয় আসছে, শীতে আসছে, দোলের ছুটিতে আসছে— দু-এক মাস অন্তর অন্তর হাজির। বাঁকড়ো তো কাছেই আসতে চাইলেই আসা যায়।”
“তারপর—?” আমি বললাম।
রত্নদিদি হাসতে হাসতে বললেন, “দেখ আমি বাহাত্তুরে বুড়ি। আমার আর লজ্জাশরম কী! যা বলব, খোলাখুলি বলব। লালমোহনের সঙ্গে আমার ভাবসাব হয়ে গেল বেশ। ও এলেই আমার ভাই মন ফুরফুর করত। চলে গেলে বুক হু হু করত। তা যাই বলিস, লালুর মামা-মামিও ভাগ্নে বলতে ছিল অজ্ঞান। ভালবাসত খুব। এই যে তাদের ভাগ্নে হরদম ফাঁক পেলেই মামার বাড়িতে ছুটে আসে— তাতে ওদের সায় ছিল, খুশি হত। কিন্তু ভাগ্নে যে কার টানে ছুটে আসে তা কি অত বুঝত! একটু-আধটু বুঝত নিশ্চয়। তারা তো কানা নয়। আমার বাপ-মাও নয়। বুঝত ঠিকই, মুখে কিছু বলত না। বলবেই বা কেন! ছেলে হবু ডাক্তার, মেয়ের বয়েস আঠারো হল। ঘরে মর্যাদায় সমান সমান। ভেতরে ভেতরে একটা সায় ছিল দু তরফের।
“তবে আমাদের সময়ে দিনকাল তো অন্যরকম ছিল। আজকালকার মতন চোখের সামনে নাচানাচি করার জো ছিল না। লুকিয়ে চুরিয়ে, এপাশ সেপাশ নজর রেখে কথাবার্তা, মেলামেশা।
“ওর তখন পরীক্ষা। শেষ পরীক্ষা। লালমোহন বইপত্তর গুছিয়ে মামার বাড়িতে পরীক্ষার পড়া করতে এল। তাই তো বলত মুখে। স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে ভিড়লে পড়া হয় না। বাড়ি সেই কোন পাড়াগাঁয়ে, বাপ জমিজায়গা, ধানচাল, পুকুর বাগান নিয়ে থাকেন।
“মামার বাড়িতে এসে লালমোহন যখন বইপত্তর খুলে বসেছে, তখন এক বিকেলে বিশ্রী কাণ্ড হয়ে গেল একটা। আমার বেশ মনে আছে দিনটা। বর্ষাকাল নয়, তবু থেকে থেকে বৃষ্টি হচ্ছিল। দিন দুপুর মেঘলা। রাতে ঘুটঘুটে অন্ধকার আর ঝিপঝিপে বৃষ্টি।
“তা সেদিন— এই মাঝ দুপুরে লালমোহন বাঁশি বাজিয়ে ডাকল আমায়। এ তোর আড়বাঁশি নয়, সিটি বাঁশি। ফুরর-ফুর—ফুরর-ফুর। চেনা বাঁশি আমার। মেঘলা দিন, দু পশলা বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে খানিকটা আগে, আমি নিজের ঘরে খাটে শুয়ে শুয়ে ‘ইন্দিরা’ পড়ছিলাম। বাবার আমার পড়ার নেশা ছিল। এক আলমারি বই, নাটক নবেল, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, দু-একটা পুরনো ইংরিজি বই—এই রকম সব। ..কাজকর্ম না থাকলে আমি চুপ করে শুয়ে থাকতাম খানিক, না হয় পুরনো পড়া বই আবার পড়তাম। সেদিন শুয়ে শুয়ে ‘ইন্দিরা’ পড়ছি। ওই যে একটা জায়গা আছে বইয়ে— ‘ধানের ক্ষেতে,/ ঢেউ উঠেছে,/ বাঁশতলাতে জল।/ আয় আয় সই, জল আনি গে/ জল আনি গে চল—’, পড়তে পড়তে হেসে মরছি নিজের মনে— এমন সময় শুনি ফুরর-ফুর, ফুরর ফুর।…বুঝলাম লালুবাবু ডাকছেন। বই রেখে উঠে পড়ে বাইরে এলাম। এদিক তাকাই ওদিক তাকাই বাঁশিওয়ালাকে দেখতে পাই না। ভর দুপুর, ঘন মেঘলা, বৃষ্টির দরুন মাঠঘাস ভিজে, চারপাশ ফাঁকা, হাসপাতালের দিকেও কেউ কোথাও নেই, দুপুরে কেউ থাকে না, বন্ধ হয়ে যায় হাসপাতাল, দুটো গোরু আর ছাগল চরছে কাঁঠালতলার দিকে। আমতলাও ফাঁকা। খুঁজতে খুঁজতে আমতলার কাছে এসে দেখি, লালুবাবু একটা আমড়ালের ওপর পাতার আড়ালে কায়দা করে আধশোয়া হয়ে বসে আছে। বসে বসে ভিজে আমপাতার পাতলা ডাল নাড়িয়ে জলের ফোঁটা ফেলছে নীচে। আমায় ভিজিয়ে দেবার আগেই সরে দাঁড়ালাম। চারপাশ দেখছি আর কথা বলছি দু জনে ; কেউ যদি আচমকা বাইরে এসে দাঁড়ায় আমাদের বাড়ির, কিংবা ডাক্তার কাকার বাড়ি থেকে— আমায় দেখতে পাবে, লালুবাবুকে পাবে না। আমায় দেখলে হয়ত ভাববে, গাছতলার নীচে কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমার ওই একটা দোষ ছিল, এটা সেটা, কানের ফুল, হারের লকেট, পয়সা কড়ি বড় হারাতাম। আমার নামই হয়ে গিয়েছিল ‘হারানি’।.. তা দু জনে গল্প করছি, কথার তো কোনো মাথামুণ্ডু থাকে না আমাদের, হঠাৎ দেখি লালুবাবু গাছের ডাল থেকে একেবারে ধপাস করে মাটিতে। শব্দ হল। পড়েই চিত। আর নড়ে না চড়ে না। চোখের পাতা বন্ধ। আমার ভাই, বুক ধড়াস করে উঠল। চারপাশ তাকিয়ে নিয়ে ওকে একবার ডাকি, একবার নাড়া দি, তবু সেই কাঠের মতন পড়ে আছে। যাঃ অজ্ঞান হয়ে গেছে বোধহয়। কী করি, আমাদের বাড়ির গায়ে ইদারার পাড়ে দড়ি বালতি পড়ে থাকে। ছুটে গিয়ে বালতির জল এনে চোখেমুখে ছিটিয়ে দিলাম। মৃগি রোগীর মতন মুখ করল একবার। তবু সাড়াশব্দ নেই। ভীষণ ভয় ধরে গেল। কী যে করি? বেঁচে আছে তো? ধারেকাছে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, সেই গোরু দুটো আর ছাগল ছাড়া। হঠাৎ আমার চোখে পড়ল, লালুবাবুর চটি জোড়া গাছতলায় পড়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় এল, জুতোর গন্ধ শোঁকালে বেহুঁশ লোকের হুঁশ ফিরে আসে শুনেছি। দৌড়ে গিয়ে একপাটি চটি কুড়িয়ে এনে লালুবাবুর নাকে চেপে ধরলাম। হাতে হাতে ফল রে ভাই। মরা মানুষ যেন জ্যান্ত হয়ে উঠল। লাফ মেরে উঠে বসল লালুবাবু। বলল, তুমি আমার মুখে জুতো ছোঁয়ালে, গোবর লাগিয়ে দিলে নাকে! কী বিচ্ছিরি গন্ধ! চললাম, আর নয়। যে মেয়ে লাভারের নাকে গোবর লাগানো জুতো ঘষে দেয়, সে মেয়ে নয়, মোষ। বলে লালুবাবু ঘেন্নায় নাকমুখ মুছতে মুছতে দে দৌড়।”
রত্নদিদি নিজেই হেসে উঠলেন। আমরাও অট্টহাসি হেসে বললাম, “জুতোটা না ঘষলেই পারতে! ইচ্ছে করে ঘষে দিয়েছিলে নাকি?”
রত্নদিদি মাথা নেড়ে বললেন, “না ভাই, বিশ্বাস কর, ইচ্ছে করে দিইনি। তাই কি কেউ দেয়! তখন কেমন মাথার গোলমাল হয়ে গিয়েছিল ভয়ে। থতমত খেয়ে গিয়েছিলুম।”
“তারপর কী হল?”
“কী হল! সে আর এক কাণ্ড। বাবুর মুখে জুতো ছোঁয়ানোর প্রায়শ্চিত্ত করতে একদিন সন্ধের মুখে আমাদের বাড়ির সদরে কাঠচাঁপা গাছটার তলায় দাঁড়িয়ে— এই তোর দু-চার পলকের জন্যে নিজের নরম গালটা এগিয়ে দিতে হল। আমি কি যেচে দিয়েছিলুম নাকি।…ও হঠাৎ বলল, তোমার গালে শুয়োপোকা পড়েছে। শিগগির দাও—ফেলে দি। ওই একটু ভুল হয়ে গেল, প্রথম, আর সেই মুহূর্তে মা এসে দাঁড়িয়েছিল বাইরে। দেখে ফেলল। লালুকে আমি ধাক্কা মেরে সরাবার আগেই সে নিজেই সরে পড়ল।”
আমাদের হাসির রোল উঠে বাইরে ছড়িয়ে পড়ল বোধ হয়।
“এ তো দেখছি—”
“দেখছি আবার কী! ওই টুকতেই সর্বনাশ হয়ে গেল।” রত্নদিদি বললেন, “লালুর পরীক্ষার পড়া হচ্ছে না ঠিকমতন বলে সে ফিরে গেল বাঁকুড়ায়। আমি থাকলাম মায়ের নজরে নজরে। ..দেখতে দেখতে মাস ফুরোল। পরীক্ষা হয়ে গেল লালুর। পাস করে হাসপাতালেই হাত পাকাতে লাগল। দেখাসাক্ষাৎ আর হয় না। শেষে লালুর মামাই বিয়ের কথাটা পাড়ল বাবার কাছে। বাবা বলল, ছেলে তো চেনাজানা, ডাক্তারও হয়েছে— ভাল কথা। তবে ওই ছেলের স্বভাবচরিত্র বুঝতে হবে। আর দেখতে হবে— ভবিষ্যৎটা কেমন? কোষ্ঠী দেখাতে হবে। বাবা নিজে দেখবে। তারপর কথা—!”
আমি বললাম, “আবার কোষ্ঠী কেন?”
“বাবার যে বিশ্বাস কোষ্ঠীতে। তখন এগুলো হত।”
“এখন আরও বেশি হয়।”
“লালুদের বাড়ি থেকে তার ছক কোষ্ঠী এল। বাবা নিজে পাঁজিপুথি নিয়ে বসল। আমার ছক গেল লালুদের বাড়িতে। …দশ বিশ দিন সময় গেল বাবার কোষ্ঠী বিচার করতে ভাল করে। তারপর বাবা বলল, এই বিয়ে হবে না। জাতকের পতন-যোগ আছে। মানে ছেলের অনিবার্য পতনযোগ। সেটাই ভীষণ খারাপ যোগ। মারকতুল্য। মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র জপতে পারে— তবে…”
আমি হেসে বললাম, “পতন-যোগ তো কেটেই গিয়েছিল, দিদি। গাছ থেকে পড়ার পর আর কিসের ভয়! অন্য পতন তো তোমার সঙ্গে, প্রেমে পতন।”
রত্নদিদি বললেন, “কে কাকে এ সব বোঝায়! বাবা ছেলের খুঁত ধরে বলল, পতন-যোগ আছে পাত্রর, তো ও-বাড়ি থেকে ছেলের বাবা বলল, মেয়ের ছক থেকে তাদের পণ্ডিত দেখেছে যে, মেয়ের বন্য জন্তু দ্বারা দংশনের যোগ আছে। অগত্যা এ-বিয়ে হবে না।”
“কিন্তু হল তো বিয়ে!”
“হল বইকি! কেমন করে হল সেটা এবার শোন।”
তিন
বিশুর মা আমাদের জন্যে চা এনেছিল। বিয়েবাড়ির কাঠের ট্রে ; ছোট ছোট কাপে কয়েক জনের মতন চা। কেউ নিলাম, কেউ নিলাম না। রত্নদিদি দু বেলা দু বারের বেশি চা খান না। তিনি চা নিলেন না। বরং আরও একবার জল খেয়ে মশলা মুখে দিলেন।
বাইরে বুঝি বসন্তের দমকা হাওয়ার ঝাপটা থেমে গিয়েছে। শীতের সিরসিরে ভাবটাই গায়ে লাগছিল। জ্যোৎস্না আরও পরিষ্কার। উজ্জ্বল।
“তারপর কী ঘটল, বলো?” আমি হেসে বললাম।
রত্নদিদি বললেন, “বলি।….তিন-চার মাস আমাদের আর দেখাদেখি নেই। চিঠিপত্তর লেখার দিনকাল তখন নয়, সে সাহসও নেই। সেই একবার যা চিঠি লিখেছিল লালুবাবু। এদিকে বিয়ের কথাও ভাঙতে চলেছে। মনটন ভাল থাকবে কেন, বল! রাগ হত খুব। ভদ্রলোকের ছেলে তুমি, একটা ভাল ছক কোষ্ঠীও করাতে পার না! বাবার মুখে কতবার শুনেছি, যদু মধু বেলা অনিলার ছক কোষ্ঠী বিচার করে বাবা মাকে বলছে, ‘বেশ ছক গো, দেরে বড় আনন্দ হল, বিয়ে হলে মিলমিশ হবে খুব, রাজযোটক।’..পরের কোষ্ঠীতে যা হবার হোক আমাদের তাতে কী! আমরা তো আর যোটক হতে পারছি না। বলবি, আমারও তো ছকটক ভাল ছিল না। আমি বলছি, মোটেই তা নয়। বাবা হল মেয়ের বাপ— সে যদি ছেলের বাড়ির লোকদের আগ বাড়িয়ে বলে, ছেলের ছকে দোষ আছে— তারাই বা মেয়ের ঘাড়ে দোষ চাপাতে ছাড়বে কেন!
“বিয়ের কথা ভেঙেই যাচ্ছিল। এমন সময় একদিন আবার লালুবাবু এসে হাজির। তার ভাবসাব দেখে মনে হল, বাড়ির গুরুজনদের কথাবার্তা নিয়ে সে একটুও মাথা ঘামায় না। বরং নতুন ডাক্তার হয়ে তার যেন চেহারা খুলেছে, আরও বড় বড় ভাব হয়েছে, আমতলায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে, যখন তখন, দিব্যি আমাদের বাড়ি এসে মাকে বলছে— মামিমা একটু চা খাওয়ান, দুধ কম, আমি আবার কড়া চা ছাড়া খেতে পারি না। কী আর বলব মাসিমা, হাসপাতালে এত খাটায় যে দিনে দশ বারো বার চা না খেলে জোর পাই না। খাটতে আমার ভালই লাগে। এই বয়েসে খাটব না তো কখন খাটব বলুন। কুঁড়েমি দেখলেই আমার মাথা বিগড়ে যায়। ওই যারা খায়দায় আর ঘুমোয়— তাদের কি হয় না।…এই ভাবে নিজের বাহাদুরি ফলায় মায়ের কাছে। আর আমায় খোঁচা মারে।”
কৃষ্ণাবউদি বলল, “বিয়ের কথা তো ভেঙেই গিয়েছে তবু উনি এভাবে আসতেন আপনাদের বাড়িতে?”
“আসবে না কেন, দু কান কাটা যে—” রত্নদিদি হেসে বললেন, “তা ছাড়া ডাক্তার কাকার ভাগ্নে, আমাদের প্রতিবেশী। দু বাড়িতে অত ভাবসাব, ডাক্তার কাকিমা মায়ের বন্ধুর মতন, লালুও আমাদের কত চেনাজানা হয়ে গিয়েছে। বিয়ের কথাবার্তা ভেঙে গেলেও একেবারে সব কিছু উপড়ে মাটিতে নুয়ে পড়েনি। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।… তা লালমোহন এবার এসে মাকে যত তোয়াজ করতে শুরু করল, তার বেশি করতে লাগল আমায়। তখন শীত পড়েছে। ওদিকে জব্বর শীত পড়ত, ভাই ; পৌষ মানে একটা লেপে কুলোত না রাত্তিরে! ভোরে তোলা জলে হাত ছোঁয়ানো যায় না, ইঁদারার টাটকা জলে ধোঁয়া ওঠে, কিন্তু যেই না—বালতির জলে বাতাস এসে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে কনকনে। সকালে সামনের মাঠটা হিনে শিশিরে ভিজে যেন অসাড় হয়ে থাকত।… রোজ সকালে দেখতাম, লালমোহন আমার ঘরের বন্ধ জানলার কাছে এসে ঠকঠক করে টোকা মারত। ধড়মড় করে উঠে বসলাম, জানলা খুললাম কী দেখি মাথার হনুমান টুপি, গায়ে ভট কম্বলের অলেস্টার, গলায় মাফলার, লালুর মুখ। তখন সবে রোদ উঠছে, সুয্যির মুখ দেখিনি, তার আগেই লালুর মুখ। তখনই ঠিক হয়ে যেত, বেলায় কোথায় কখন দু জনে দেখা হবে। আবার বেলায় যখন দেখা হত, বলে দিত বিকেলে কেমন করে দেখা হবে। এই ভাবে সারা দিনে তিন-চার বার দেখা হত দু জনে আড়ালে। কখনো কাঁঠালতলার পেছনে একটা অকেজো রোড রোলারের আড়ালে। কখনো বন্ধ হাসপাতালের পেছনে করবী ঝোপের কাছে। লালু আমায় বলত, একেবারেই ঘাবড়াবে না, বিয়ে আমাদের হবেই, কেউ আটকাতে পারবে না ; আমি আর এক সেট কুষ্ঠীগুষ্টি করিয়ে দিচ্ছি বাঁকড়োর ফেমাস পণ্ডিতকে দিয়ে, হরিসাধন জ্যোতিষার্ণব। দেখবে সেই কুষ্ঠীতে আমি রাজা, তুমি রানি। …আর তখনও যদি তোমার বাবা বাগড়া মারেন, তোমায় নিয়ে আমি পালাব রতনমণি। সেরেফ ক’টা মাস। আমি চাকরির চেষ্টায় আছি। তুমি লক্ষ্মী, একটু সবুর করো, সবুরে মেওয়া ফলে।”
‘ক’ মাস লাগল মেওয়া ফলতে?” আমি বললাম হাসতে হাসতে।
“তা লাগল ক’মাস। তার আগে এক কাণ্ড হল। লালুবাবু যে সেবার একটা বাক্স ক্যামেরা নিয়ে এসেছে ফটো তুলবে বলে, আমায় বলেছিল। ফটোও তুলত, আমি নজর করিনি। একদিন বলল, আমার একটা ছবি তুলবে। আমি না না করলাম। কিন্তু সে একেবারে নাছোড়বান্দা। শেষে একদিন শীতের দুপুরে, কেউ যখন কোথাও নেই, হাসপাতালের পেছনের সেই করবী ঝোপের পাশে একটা পাথরের ওপর বসাল আমায় লালু। বলল, সে সব ব্যবস্থা করে ক্যামেরাটা মানির হাতে দেবে। নিজে থাকবে আমার পাশে, ফটো তুলবে মানি। আমি কিছুতেই রাজি হচ্ছিলাম না। লালুবাবুও শুনবে না। শেষে আমার পা ধরতে আসে। কী করা করব, রাজি হয়ে গেলাম।”
“ফটোও তোলা হল যুগলের?”
“হল। কিন্তু শয়তানিটা কী করল জানিস লালমোহন।” রত্নদিদি বললেন, “মানিকে ঠিকঠাক দাঁড় করিয়ে দিয়ে নিজে একবার সব দেখে নিয়ে আমার পেছনে এসে দাঁড়াল। আমার ভাই লজ্জাই করছিল। মুখ তুলে তাকাতে পারি না। ওদিকে মানিকে রেডি হতে বলে লালুচাঁদ পেছন থেকে ঝপ করে আমার চোখ টিপে ধরল। আর ওদিকে ছবি তোলাও হয়ে গেল মানির। ফটো তুলে নিয়ে মানি দে ছুট। আমি হতভম্ব। বুঝলাম, মানিকে সবটাই শেখানো পড়ানো ছিল। রাগের মাথায় লালুর হাত খামচে, মাথার চুল টেনে ছিড়ে যা মুখে এল বলতে বলতে বাড়ি ফিরে এলাম। রাগে আমার কান্না পেয়ে যাচ্ছিল।”
রত্নদিদি একটু চুপ করলেন। কিছু যেন ভাবছিলেন।
বললাম হেসে, “ফটোটা উঠেছিল?”
“উঠেছিল মানে, কপালে থাকলে কী না ওঠে রে? লটারির টাকাও উঠে যায় চাপরাশির কপালে। মানির হাতে তোলা সেই ফটোও লালমোহনের কপালে উঠে গেল। ..তা ভাই বলতে পারিস, ফটোটা উঠল বলে বিয়ের ফাঁসটাও লেগে যেতে পারল।”
“কী রকম?”
“রকম আর কী! লালুবাবু চৌখস ছেলে। বাঁকড়াতে থাকতে থাকতেই বি.এন রেলের হাসপাতালে চাকরি জোগাড় করে ফেলল ছোট ডাক্তারের। তারপর একদিন বাবার নামে এক রেজিস্ট্রি এল। নতুন ছক কোষ্ঠী আর পাঠাবার দরকার হয়নি ওর। শুধু ওই ছবির একটা কপি পাঠিয়ে দিল বাবাকে, আর লিখল— ‘আপনাদের বিবেচনায় যা হয় করিবেন। আমি দূরে চলিয়া যাইতেছি, নতুন চাকরি, বিলম্বে আমার অসুবিধা হইবে।”
“বলো কি, সেই ফটো তোমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিল?”
“দেবার জন্যই তো তুলেছিল। কম সেয়ানা নাকি ও। মাথায় যত ফন্দিফিকির তত বুদ্ধি। আইবুড়ো এক মেয়ের অমন ছবি, পেছন থেকে চোখ চেপে ধরে আছে এক ছোঁড়া— ওই ছবি দেখার পর কোন বাপ-মা আর বসে থাকতে পারে? অন্য সম্বন্ধ-ই বা করবে কেমন করে! কোন সাহসে! কাজেই বিয়েটা হয়ে গেল।” রত্নদিদি হাসলেন, “লালুবাবুর রত্নলাভ হল।”
“বিয়েতে খুব ধুম হয়েছিল তাই না!” কে যেন বলল মেয়েদের তরফ থেকে।
“তা হয়েছিল। তবে তাদের আজকাল যেমন দেখলাম তেমন নয়। সে অন্য রকম, নিজেদের লোকজন, পাড়াপড়শি নিয়ে ধুম। বিয়ের পর অষ্টমঙ্গলা সেরে বরের সঙ্গে চলে গেলাম দূরে। সেখান থেকে চাকরির বদলি ঘটতে ঘটতে আটশো হাজার মাইল দূরে গিয়েই পড়লাম একদিন। আমাদের আর এদিকে ফেরা হল না। তারপর একদিন তোদের জামাইবাবু তো চলে গেলেন। আমিই পড়ে থাকলাম ছেলে বউ নাতি আগলে। কী করব বল? কপালে আমার যেমনটি লেখা ছিল সেই ভাবেই আছি। দুঃখ করে কী লাভ!”
সবাই চুপ। একটু যেন গম্ভীর হয়ে এল আবহাওয়া। অবস্থাটা হালকা করার জন্য আমি বললাম, “তা সেই ফটোটা তুমি রেখেছ না হারিয়ে ফেলেছ?
মাথা নেড়ে রত্নদিদি বললেন, “হারিয়ে ফেলব কেন, রেখে দিয়েছি। তা বলে সেটা কি আর, দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখা যায়! লোকে দেখলে বলবে কী। ছেলেরাও তো বড় হয়ে উঠছিল। আমার বাক্সর তলায় লুকিয়ে রেখে দিতাম।”
“আহা, রত্নদিদি— সে ফটো যদি একবার দেখতে পেতাম…।”
“পাগল, তোদের দেখাতাম আর কী!…এবারই কি হল জানিস! শীতের আগে একদিন আমার তোরঙ্গ খুলে চাদরটা জামাটা বার করছি রোদে দেব বলে। আমাদের ওখানে শীত একেবারে কসাই, মায়াদয়া নেই, পড়ল তো গা-হাত-পা কেটে কেটে রক্ত বার করে দেয়।…তা আমি তোরঙ্গ খুলে আমার শালটা চাদরটা ফ্ল্যানেলের জামাটা বার করছি, করতে করতে তোরঙ্গর তলায় রাখা ফটোটা হাতে এল। তুলে নিয়ে দেখছিলাম। কত পুরনো ছবি, মামুলি একটা ক্যামেরায়, ছবিটা হলুদ হয়ে গিয়েছে। বেসম-বেসম রং, এখানে ওখানে দাগ ধরেছে। উঠে গিয়েছে খানিক— তবু ঘটিহাতা জামা পরা বিনুনি ঝোলানো রোগা পাতলা একটা মেয়েকে চোখে পড়ে, আর পড়ে খোঁচা খোঁচা মাথার চুলের একটা ছেলেকে, মালকোঁচা মারা ধুতি, গায়ে শার্ট আর হাতকাটা সোয়েটার। ছেলেটা মেয়েটার পেছনে দাঁড়িয়ে। চোখ টিপে ধরে আছে মেয়েটার। ও ছবি দেখলে কেউ তোদের রত্নদিদির ছবি বলবে না। তোদের জামাইবাবুরও নয়।…নিজের মনে ছবিটা দেখে নিজেই বুঝি হাসছিলাম, এমন সময় হুড়মুড় করে নাতি এসে পড়ল। ফটোটা লুকোতে গিয়েও পারলাম না। নাতি কেড়ে নিল। দেখল খানিক। তারপর কী বলল জানিস?”
“কী” ?
“বলল, এ বুড়িয়া কার পিকচার এটা?..কী বলি বল নাতিকে? বললাম, ও এমনি। হবে কারও। বাক্সর মধ্যে পড়েছিল।..তা ফটোটা ফেরত দিতে দিতে নাতি বলল, বুঢড্ডি টিভিতে ওল্ড হিন্দি ফিল্ম দেখায় দেখেছ? অছ্যুত কন্যা, ঝুলন– দ্যাট টাইপ…বেচারি হিরো হিরোইন…ফালতু, আদ্মি! একদম ফালতু! বলে সে চলে গেল। …আমি আর কী করব বল! দেখলাম একটু, তারপর কাগজে মুড়ে— যেমনটি ছিল তোরঙ্গর তলায় রেখে দিলুম।…ভাবিস না আমার রাগ দুঃখ হল! কেনই বা হবে ভাই! পঞ্চান্ন ষাট বছর কী কম! অত পুরনো ছবির দাম কী! কদরই বা হবে কেন? নাতিই বা কেমন করে চিনে নেবে তার ঠাকুমা ঠাকুরদাকে ওই ফটো থেকে! চেনা যে যায় না। ”
রত্নদিদি চুপ করে গেলেন। আমরাও চুপচাপ। ততক্ষণে দিদির মাথার ধ্বধবে সাদা চুলের ওপাশে জানলা ঘেঁষে এক ঝলক জ্যোৎস্না এসেছে। মনে হচ্ছিল, আলোটা যেন রত্নদিদির মাথায় মাখানো। সামান্য পরে মুখেও নেমে আসবে।
হঠাৎ দেখি রত্নদিদি একটু হাসলেন। বললেন, “আবার কী মনে হয় জানিস এক একবার। নাতি হয়ত কিছু একটা আন্দাজ করেছিল। করেও আমার সঙ্গে দুষ্টুমি করল। ওটা কী কম পাজি, না, ধুরন্ধর। কেমন ঠাকুরদার নাতি দেখতে হবে তো!”
রসাতল
মহেশ ঘোষ খানিকটা আগে আগেই বাড়ি ফিরলেন। মন ভার, মুখ ভার। নিজের ঘরে এসে দেখলেন, স্ত্রী নবতারা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুঠো মুঠো পাউডার ছড়াচ্ছেন গায়ে। মাথার চুল ঝুঁটি করে বাঁধা, চুড়োর মতন। ঘাড়ে গলায় চাপ চাপ পাউডার ; সারা মুখ সাদা। হাতে বুকেও অজস্র পাউডার ; পায়ের তলায় মেঝেতেও পাউডারের গুঁড়ো ছড়িয়ে আছে।
মহেশ কয়েক পলক আলমারির আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। আলমারিটা তাঁর বাবার আমলের। পয়লা নম্বর বর্মি টিক দিয়ে তৈরি, ইংলিশ ডিজাইন। আলমারির একটা পাল্লায় আসল বেলজিয়াম গ্লাস। পুরোটাই। আয়নায় স্ত্রীকে আপাদমস্তক দেখা যাচ্ছিল, শাড়ির আঁচল ভূলুণ্ঠিত, গায়ের জামাটা ঢোল্লা নিমা ধরনের।
আলমারির মতন তাঁর এই স্ত্রীটিও বাবার আমলের। বাবাই এনে ঘরে ঢুকিয়েছিলেন। উনিও বর্মি। তবে আসল নয়। রেঙ্গুনে জন্ম, দিল্লিতে বালিকা জীবন, কলকাতায় যৌবন-সমাগম, তার পর দুর্গাপুরে এসে বিবাহযোগ্যা কন্যা। বাবার কৃপায় তখন থেকেই উনি মহেশের সহধর্মিণী। নবতারা নামটি থেকে ‘নব’-টি কবে খসে গেছে। এখন উনি ‘তারা’। অবশ্য মাঝে মাঝে মহেশ সোহাগ করে স্ত্রীকে তারাসুন্দরী বলে ডাকেন।
আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, গায়ের আঁচল মাটিতে লুটিয়ে মহেশের তারাসুন্দরী পাউডার মাখছেন, ঘরের দু’কোণের দুটো পাখাই ঝড়ের বেগে ঘুরছে, পাউডার উড়ছে বাতাসে, লেবু-লেবু গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে, বাতি অবশ্য একটাই জ্বলছিল। এমন একটি দৃশ্য অন্য দিন দেখলে মহেশ হয়ত গান গেয়ে উঠতেন, আহা কী শোভা দেখ রে, মাচা তলে রাধা সাজে বাহা রে। আজ আর গান এল না গলায়, অন্য কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন—তার আগেই নবতারা কথা বললেন। “আজ এত তাড়াতাড়ি?”
গায়ের জামা আলগা করতে করতে মহেশ বললেন, “চলে এলাম।”
“চলে এলে! তাসপাশা জমল না?” বলতে বলতে নবতারা মুখের ওপর জমা পুরু-পাউডার আলতো করে মুছে নিলেন। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন দেওয়াল-ঘড়িটা। হিসেব তাঁর ভুল হয়নি। এখন মাত্র সোয়া আট। ঘোষবাবু রাত সাড়ে নয় কি দশের আগে বড় একটা বাড়ি ফেরেন না। আজ আগে আগেই ফিরেছেন।
মহেশ গায়ের জামা খুলে জায়গা মতন রাখতে রাখতে বললেন, “এ-মাসে ক’কৌটো হল? ছয় না সাত?”
কথাটা শুনেছিলেন নবতারা। জামার তলায় আরও খানিকটা পাউডার ছড়িয়ে বললেন, “কেন? হিসেব চাইছ?”
‘না। হিসেব চাইছি না। হিসেবের দিন ফুরিয়ে গেছে। এবার নিকেশ।.. আহা, কী চেহারাই হয়েছে এ-সংসারের। বাড়িতে ঢুকলাম, নীচে তোমার ছোট ছেলে আর মেয়ে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আড্ডা জমিয়েছে। গান শুনছে—ইংরিজি গান। আই লাভ ইউ বেবি। স্টিরিও ফেটে যাবার জোগাড়। ও তো গান নয়, কামান। …আর ওপরে এসে দেখি—তুমি বন বন করে দুটো পাখা চালিয়ে বাঘের মতন থাবা করে পাউডার মাখছ। বাঃ, বেশ!”
লুটোনো শাড়ির আঁচল তুলে নিতে নিতে নবতারা বললেন, “তাতে হয়েছে কী? দুটো পাখা চললে আর দু’কৌটো পাউডার খরচ হলে তুমি কি ফতুর হয়ে যাচ্ছ! নিজে যখন দু’বোতল গিলে আস—তখন হিসেবটা মনে থাকে না।”
“বাজে কথা বোলো না। বোতল আমি গিলি না।” “না, তুমি গেলো না বোতল তোমায় গেলায়। ’’
“আবার বাজে কথা। মাসকাবারি বাজারে দু’চারটে বাড়তি জিনিস তোমার সংসারে আসে না? আমাদেরও ওই রকম মাসকাবারি হিসেব। তুলসীরই যা রোজকার বাজার।”
“আমারই বা নিত্যি দিনের নাকি! গরমে মরছি, বুকপিঠ ঘাড়গলা জ্বলে যাচ্ছে ঘামাচিতে, দু’কৌটো পাউডার যদি মেখেই থাকি—তোমার এত খোঁটা দেবার কী আছে! না হয় তোমার পয়সায় মাখব না আর, ছেলের পয়সায় মাখব।”
“থাক, তোমার ছেলেদের বহর বোঝা গেছে। বড়টি তো টু-ইন-ওয়ান হয়ে আছেন। তাঁরা দুটো মানুষ থাকেন—তাতেই বাবু-বিবির চলে না, যখন-তখন ভরতুকি পাঠাতে হয়।”
“আমার ছেলে…”
“তিন হাজারি। তিনে এখন কিছু হয় না। বাইরে থাকেন তো! ছেলে, ছেলের বউয়েরও কুলোয় না ওতে। বাপের ভরতুকিটা হল ওদের ঠেকো। যাক গে, তুমি মাখো। গরমে ঘামাচি, শীতে পা-ফাটার ক্রিম…”
“তার মানে! ঘামাচিতে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে না বলছ?”
“তা বলিনি। বলছি ঘামাচি আর বেঙাচি একই ক্লাসের। ও যায় না।”
“কিসে যায়?”
“নিজেই যাবে। এই তো বর্ষা পড়ে গেল। এবার যাবে।”
“ও! খুব টেরা টেরা কথা বলছ যে আজ—!” নবতারা আলমারির কাছ থেকে সরে এলেন। স্বামীকে দেখতে লাগলেন খুঁটিয়ে। নেশার কোনও চিহ্ন নেই। বরং অন্য অন্য দিন মুখের যেমন স্বাভাবিক ভাব থাকে, আজ তা নেই। খানিকটা গম্ভীর মুখ। কপালটাও কোঁচকানো সামান্য। আড্ডা-ফেরত স্বামীকে বেশিরভাগ সময়েই হাসিখুশি মজাদার লাগে, যেন আড্ডার রেশ নিয়েই বাড়ি ফেরেন। আজ ঘোষবাবুর মুখের এ-চেহারা কেন! নবতারা বললেন, “কী হয়েছে? ঝগড়াঝাটি?”
“ঝগড়াঝাটি! বন্ধুদের সঙ্গে আমি ঝগড়া করব?”
“তাস খেলতে খেলতে তো করো। “
“সে খেলার ঝগড়া।’’
“তা হলে হয়েছে কী? আসর ভেঙে চলে এলে?”
মহেশ ততক্ষণে কলঘরে যাবার জন্যে তৈরি। হাতমুখ ধুয়ে এসে বসবেন আরাম করে ; কাপড় বদলানো হয়ে গিয়েছে।
“তা হলে?” আবার বললেন নবতারা।
জবাব দেবার আগে মহেশ ডান হাতটা পায়ের দিকে ঝুলিয়ে আঙুল দিয়ে মাটি দেখালেন। বললেন, “শেষ।… আমার এখন রসাতল অবস্থা। রসাতল গমন।”
নবতারা কিছুই বুঝলেন না। অবাক হয়ে বললেন, “কী গমন?” “রসাতল। মানে মরণদশা। সাত-আট নয়—ব্যাস…”
নবতারার মাথাটি বেশ গোলগাল। তা যত গোলই হোক, দেহের অন্যান্য অঙ্গ ও অংশ যে-পরিমাণ গোলাকার তার তুলনায় কিছুই নয়। পাকা, আধপাকা চুল ও গোল মাথা নিয়েও নবতারা কথাটার অর্থ ধরতে পারলেন না। বললেন, “কী বলছ রসাতল ফসাতল! কিসের মরণদশা?”
“আমি বলেছি নাকি! যা বলেছে তাই বলছি। বলেছে, রসাতল অবস্থা। মরণদশা। সাত আট নয়…ব্যাস। শেষ।” বলতে বলতে পায়ে চটি গলিয়ে মহেশ এগিয়ে যাচ্ছিলেন দরজার দিকে।
নবতারা স্বামীর হাত ধরে ফেললেন। “কে বলেছে?”
“চু চে চোল। মানে তিব্বতি বাবা!”
“সে আবার কে? তিব্বতি বাবাটা পেলে কোথায়?”
“নন্দর বাড়িতে। নন্দর কেমন ভাই হয়। পাঁচ বছর তিব্বতে আর তিন বছর ভুটানে ছিল। ওদিককার তন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ। বড় বড় জটা, মানে ওই ক্লাসের চুল, ইয়া দাড়ি-গোঁফ, চোখ দুটো একেবারে ছুরির মতন। না, চোখ দুটো বড় বড় গোল গোল—কিন্তু দৃষ্টিটা ছুরির মতন।”
নবতারা বললেন, “তুমি আমায় ভয় দেখাচ্ছ?”
“আমি তোমায় ভয় দেখাব! আমার ঘাড়ে ক’টা মাথা। নিজেই আমি ভয় পেয়ে গেছি। রসাতল অবস্থাটা বুঝছ না? কী ভয়াবহ দশা!”
“বুঝছি। বেশ বুঝছি,” নবতারা বলেন, “তোমার সঙ্গে চল্লিশ বছর ঘর করে রসাতল বুঝব না!”
“কী কপাল আমার! তা আর একটা ঘর যদি আগে হত—, ইস! আমার কাউন্ট হত চার-পাঁচ-ছয়। ফোর ফাইভ সিক্স। তখন থাকত চ্যারিয়ট—রথারোহণ অবস্থা। তাতে ধনলাভ পুত্রলাভ।”
নবতারা স্বামীকে দেখলেন, নাকমুখ কুঁচকে বললেন, “ধনলাভ পুত্রলাভ। চৌষট্টি বছরের বুড়োর এখনও শখ কত! পুত্রলাভ! তোমার লজ্জা করে না! এ জন্মে আর রথে চড়তে হবে না, পরের জন্মে চড়ো।” হাত ছেড়ে দিলেন নবতারা।
মহেশ বললেন, “পরের জন্মের কথা বলতে পারছি না। এ-জন্ম শেষ হয়ে এল গো, সাত আট নয়—মানে আর টেনেটুনে সাত আর আটে পনেরো প্লাস নয়—মানে চব্বিশ। মাত্তর চব্বিশ মাস ; দু’বছর। তারপরই ফট।” বলতে বলতে তিনি বাইরে চলে গেলেন।
নবতারা যেমন ধাঁধায় পড়ে কিছুই বুঝতে পারছিলেন না—সেইভাবেই হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেন।
তাঁর স্বামীর বয়েস চৌষট্টি। মানে পঁয়ষট্টিতে সবেই পড়েছেন। শরীর স্বাস্থ্যে কোনও গোলমাল নেই। এই বয়েসে ছোটখাটো যেসব গোলমাল থাকা স্বাভাবিক—তার ছ’আনাও নয়। বেশ মজবুত রয়েছেন ঘোষবাবু। এখনও হপ্তায় দু’দিন মাংস খান, আধ সেরের কাছাকাছি দুধ খান রাত্রে, খাওয়ায় অরুচি নেই, নিজে হাটবাজার করেন, বাগান নিয়ে বসেন প্রায়ই, চারবেলা খবর শোনেন রেডিয়োয়, তাসপাশা খেলেন বন্ধুদের সঙ্গে, বই টইও পড়েন রোজ দু-পাঁচ পাতা। স্ত্রীর সঙ্গে গলাবাজি গলা জড়াজড়ি দুইই হয়, ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ফক্কুড়ি করতেও আটকায় না। এই মানুষটির এমন কিছুই হয়নি যে, মরণদশা ঘনিয়ে আসবে! তাও কিনা দু’বছরের মধ্যে। কিসের রসাতল? কে এই তিব্বতি বাবা? লোকটা তো অদ্ভুত! সুস্থ সমর্থ, প্রাণবন্ত একটা বয়স্ক মানুষকে রসাতল দেখিয়ে দিল!
নন্দবাবুকে বিলক্ষণ চেনেন নবতারা। স্বামীর বন্ধু। শিবতলার দিকে বাড়ি। এখানকার পুরনো লোক, মহেশবাবুর মতনই। নন্দবাবুর স্ত্রী নেই। বছর চারেক হল মারা গেছেন মহিলা। নবতারার সঙ্গে ভাল রকম মাখামাখি ছিল। পারিবারিক বন্ধুত্ব ছিল দুই পরিবারের। স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকেই নবাবুর খানিকটা অন্য রকম মতি হয়েছে। সাধু সন্ন্যাসী, বাবাজি, হাত দেখা, কপাল গোনা থেকে শুরু করে প্ল্যানচেট আত্মা নামানো পর্যন্ত। স্বামীর কাছেই সব খবর পান নবতারা। ঘোষবাবু নিজেই বলেন, ‘নন্দটার মাথাটা গেছে একেবারে। যত রাজ্যের সাধু-সন্ন্যাসী, আখড়া আশ্রম, তান্ত্রিক, ধুনোবাজি! ওই পিডি-ই মাথাটা খেয়েছে ওর।’ পিডি মানে প্রফুল্ল দত্ত, যাকে মহেশরা ঠাট্টা করে বলেন, পিণ্ডি দত্ত। প্রফুল্ল দত্তর ও-সব আছে, আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক ব্যাপার-স্যাপারে টান আছে। লাইনটা জানে।
স্বামী সম্পর্কে সামান্য উৎকণ্ঠা বোধ করলেন নবতারা। ঘোষবাবুর কোনও কালেই এসব ছিল না। হঠাৎ এত ঘাবড়ে গেলেন? উৎকণ্ঠার বেশি কৌতুহলই হচ্ছিল নবতারার।
বিছানায় বসেছিলেন স্বামী-স্ত্রী। মাথার দিকে মহেশ, পায়ের দিকে নবতারা। মহেশের পরনে হাই কোয়ালিটি লুঙ্গি, গায়ে বোতামঅলা সাবেকি গেঞ্জি। হাতে সিগারেট। নবতারার মুখে ছাঁচি পান। ভাগ্নে এসেছিল কাল, মাসিকে শ’খানেক পান দিয়ে গেছে। বেনারসি ছাঁচি পান। নবতারা ছাঁচি পান আর জরদা মুখে বসেছিলেন।
পান চিবোত চিবোতে নবতারা এক সময় বললেন, “এবার বলল, শুনি। নন্দবাবুর বাড়িতে কে কে ছিলে তোমরা?”
মহেশ অল্পক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বললেন, “কে কে ছিলাম! ছিলাম সবাই—যেমন থাকি। নন্দ, তুলসী, কেষ্ট…। ভবেন ছিল না।”
“তাসপাশা খেলনি?”
“খেলতে বসার আগেই নন্দ তার ভাইকে ভেতর থেকে ধরে আনল আলাপ করিয়ে দিতে।”
“কেমন ভাই?”
“নিজের নয় ; জ্ঞাতি সম্পর্কে ভাই।’’
“তবে তো বাঙালি!”
“বাঙালি ছাড়া আবার কী! তবে পাঁচ বছর তিব্বত আর দু-তিন বছর ভুটানে থাকতে থাকতে চেহারাটা কেমন লামা-টাইপের হয়ে গেছে।”
“নাম কী?”
“বাঙালি নাম চুনি। ডাক নাম। নন্দ তো চুনি বলেই ডাকছিল। ইয়ের নাম চু চে চোল না কী যেন।”
“ইয়ের নাম মানে?”
“সিদ্ধির নাম। তিব্বতে টাইটেল পাওয়া। মানে চুনি যখন তিব্বতে ওদের মতন করে তন্ত্রসাধনা করে সিদ্ধিলাভ করল তখন থেকে নাম হল চু চে চোল।”
“তিব্বতি গণৎকার?”
“না, ও হল—ইন্দো তিব্বত অ্যাসট্রলজার। আমরা ছেলেবেলায় কলকাতায় মামার বাড়িতে গেলে ইন্দো-বর্মা রেস্টুরেন্টে ঠোস, কাটলিস, চ্চা খেতাম; ভেরি ফাইন। সেই রকম ও ইন্দো-তিব্বতি জ্যোতিষী এবং তান্ত্রিক। দু’রকম মতটত মিলিয়ে এখন তিব্বতি বাবা।”
“বাংলাতেই কথা বলল তো?”
“আবার কিসে বলবে! পেটে বাংলা। মাঝে মাঝে দু’চারটে তিব্বতি ঝাড়ছিল।”
“বয়েস কত?”
“ব-য়েস! বয়েস আর কত, আমাদের চেয়ে ছোট, নন্দর ছোট ভাই না। নন্দ আমার চেয়ে চার বছরের ছোট, ওই ভাই আরও খানিকটা হবে। ধরো, ছাপান্ন, সাতান্ন। কিন্তু চেহারা দেখলে মনে হয় পঞ্চাশটঞ্চাশ। বেটার মুখটা ছুঁচলো, রুইতনের মতন, লম্বা নাক, ধকধক করছে চোখ, লালচে রং। গায়ে একটা চিত্র বিচিত্র আলখাল্লা। ইয়া লম্বা লম্বা চুল মাথায়, দাড়ি গোঁফের জঙ্গল।” মহেশ সিগারেটের টুকরোটা ছাইদানে ফেলে দিলেন।
নবতারার কান খুব সজাগ। তবু তিনি খানিকটা সরে এলেন স্বামীর কাছে। বললেন, “তা হঠাৎ তোমার কুষ্টি নিয়ে পড়ল কেন?”
“কোষ্ঠী নয়। এ আমাদের বারো ঘর স্টাইলের কোষ্ঠী নয়। অন্য ক্যালকুলেশান। নন্দ বলল, আমার সম্বন্ধে কিছু ফোরকাস্ট করবে। লোকটা তখন আমার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল ; তারপর কাগজ পেনসিল চেয়ে নিয়ে ফটাফট কী দাগটাগ মারল কাগজে। লিখল এটা সেটা। ক্যালকুলেশান করল। করে বলল, আমার রসাতল অবস্থা চলছে। মানে মরণদশা। সাত আট নয়ের হিসেব করলে আর মাত্র চব্বিশ মাস, মানে মাত্তর দুটি বছর। তার পরেই ফট।”
“ফট! বললেই হল! কেন ফট!”
“তা তো জানি না। তবে আমি বেটার কথায় হেসে উঠতেই, ও আসছি বলে ভেতরে চলে গেল। ফিরে এল একটা বেতের চৌকো ঝুড়ি নিয়ে। চামড়ার স্ট্র্যাপ-বাঁধা ঝুড়ি। ওপরে রং। মস্ত এক সাপের মুখ আঁকা।”
নবতারা আরও দু হাত সরে এলেন স্বামীর দিকে। “ঝুড়ি কী হবে?”
“ঝুড়ির মধ্যেই ছিল জিনিসটা।… ঝুড়ি ঘেঁটে ওই বেটা গোটা কয়েক আয়না বার করল।”
“আয়না!” নবতারা অবাক হয়ে গালে হাত তুললেন। “আয়না কেন?”
“কেন—তা কি আমি আগে বুঝেছি ছাই। আয়নাগুলো ছোট ছোট, ইঞ্চি তিনেক লম্বা হবে। চওড়ায় দু ইঞ্চির মতন। রাস্তার নাপতেদের মতন। অবশ্য গালার ফ্রেম দিয়ে বাঁধানেনা। একটা আয়না আমায় দিল লোকটা। বলল, দেখুন।”
“তুমি দেখলে?”
“দেখার আগে কী হল শোনো। আগে আমার দু চোখে সুর্মা মতন কী লাগিয়ে দিল। চোখ জ্বলে যায় আমার। গন্ধও নাকে লাগছিল। জল এসে গেল চোখে। তারপর আয়নাটা দেখলাম। ঝাপসা ভুসোওঠা কাচ। এবড়ো খেবড়ো। কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না প্রথমে, তারপর দেখলাম আয়নার তলা থেকে একটা চিতার ছবি ফুটে উঠল। লকলক করে আগুন জ্বলছে। সবই ঝাপসা, তবু দেখলাম। যত ভাল করে দেখার চেষ্টা করি ততই চিতাটা জ্বলজ্বলিয়ে ওঠে।’’
নবতারা ঘামাচির জ্বালা ভুলে গেলেন। আগে মাঝে মাঝে গলা ঘাড় বুক চুকোচ্ছিলেন, এখন আর হাত নড়ল না।
মহেশ বললেন, “ওই তিব্বতি বেটা বলল, ওটাই আমার ভবিষ্যৎ। রসাতলের শেষ অবস্থা। সাত আট নয়-এর শেষ কাউন্ট।”
নবতারা বার দুই ঢোঁক গিলে হঠাৎ বললেন, “চিতা জ্বলছিল জ্বলুক, তুমি তো আর নিজেকে দেখোনি। তবে?”
মহেশ বললেন, “মনে করতে পারছি না। যা চোখ জ্বলছিল।”
নবতারা অনেকক্ষণ কথা বললেন না। শেষে আরও খানিকটা এগিয়ে এসে শাড়ির আঁচল দিয়ে মহেশের কপাল মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন, “রাস্তার লোকের কথায় তুমি এত ঘাবড়ে গেলে। কে না কে ওই তিব্বতি বাবা, বুজরুকি করল, আর তুমিও নেতিয়ে পড়লে!… দাঁড়াও আমি দেখছি নন্দবাবুকে। বাড়িতে ডেকে এনে যা করব—বুঝিয়ে দেব, আমি কে। ওসব তিব্বতি বুজরুকি আমার কাছে চলবে না। রসাতল দশা। দেখাচ্ছি রসাতল। কার রসাতল তখন বুঝবে!”
“নন্দর কী দোষ!”
“নন্দর ভাইটাকেও ছাড়ব নাকি! দেখো কী করি। যত্ত সব বুজরুক। বুড়ো হচ্ছে যত ততই ভীমরতি বাড়ছে।… নাও চলো, দশটা বেজে গেল, খেতে চলো।” বলে স্বামীর হাত ধরে টানলেন নবতারা।
দুই
দিন দুই পরে নন্দ এলেন। সন্ধেবেলায়। বসার ঘরে বসে বসে মহেশের সঙ্গে কথা বলছেন, চা আর হিঙের কচুরি এল। নবতারা নিজেই হাতে করে নিয়ে এসেছেন। বাইরে বৃষ্টিও নামল। বর্ষার শুরু তো, এক আধ পশলা রোজই হচ্ছে।
নন্দ বললেন, “আসুন বউদি।… আপনি শুনলাম ডেকে পাঠিয়েছেন।”
নবতারা হাসিমুখ করে বললেন, “তা কী করব বলুন! আপনারা তো আর আসেনই না। পথ ভুলে গেছেন। ডেকে না পাঠালে কী আস্তেন! নিন—আগে চাটুকু খেয়ে নিন।”
একসময়ে নন্দলালের খাদ্যরসিক বলে খ্যাতি ছিল। পুরুষ মানুষ হয়েও তাঁর শখ আর নেশা ছিল রান্নাবান্নার। নিজের হাতে নানারকম আমিষ রান্না রাঁধতে পারতেন। খাওয়াতেন বন্ধুবান্ধবকে ডেকে। স্ত্রী মারা যাবার পর তাঁর শখ ঘুচে গিয়েছে, অরুচি এসেছে খাওয়া-দাওয়ায়। জিবের স্বাদ নিয়ে আর মাথা ঘামান না, পেটে দুটো পড়লেই হল।
কচুরি খেতে খেতে নন্দ বললেন, “নিজে করেছেন? বেশ হয়েছে…! আপনার হাতের সেই ছানার তরকারি আর পায়েস ভুলতে পারি না।”
মহেশ বললেন, “তুমি মাঝেমাঝে এসে বললেই, তোমার বউদি পায়েসটা, ছানাটা খাওয়াতে পারে। “ বলতে বলতে আরও আধখানা কচুরি মুখে পুরে দিলেন।
নবতারা বললেন, “তা পারি। কিন্তু উনি আসেন কোথায়?”
“কেন। আসি তো! অবশ্য কমই।… আসলে কি জানেন বউদি, দাদার কাছ থেকে রোজই আপনাদের সব খবর পাই, বিনুর সঙ্গেও দেখা হয়ে যায়। কাজেই আর—” বিনু মানে বিনতা, মহেশদের মেয়ে।
নন্দর কথা শেষ হবার মুখেই নবতারা বললেন—”আপনার দাদার তো খাওয়া-দাওয়া ঘুম গেল।”
“কেন কেন?”
“সে তো আপনিই ভাল জানেন! আপনার কোন ভাই, তিব্বতি বাবা নাকি বলেছে, ওঁর এখন রসাতল অবস্থা। মানে ইয়ের দশায় পেয়েছে…” বলে স্বামীর দিকে তাকালেন নবতারা।
“মরণদশা,” মহেশ বললেন, “সাত আট নয়। মাত্র আর দু বছর।”
নন্দ মাথা নাড়লেন। “হ্যাঁ, দশাটা খুব খারাপ। চুনি তাই বলল।”
“আপনার চুনি কি জ্যোতিষী?”
“জ্যোতিষী! ওরে বাব্বা, সে তো এখন ত্রিতন্ত্রসিদ্ধ পুরুষ। অর্ডিনারি জ্যোতিষী ওর কাছে লাগে না। তিন ধাপ ওপরে। চুনির ভীষণ পাওয়ার। দৈব-ক্ষমতা পেয়েছে। মুখ থেকে যা খসে, তাই হয়।”
নবতারা বললেন, “কী দেখে আপনার ভাই বুঝল ওঁর এমন একটা অবস্থা হয়েছে! কুষ্টি তো দেখেনি যে বলবে—!”
হাত নেড়ে নন্দ বলল, “কোষ্ঠীর দরকার করে না। এ অন্য হিসেব।”
“কী হিসেব?”
“আমি তা জানি না, বউদি। তবে কোষ্ঠীর রকমফের আছে। এক এক দেশে এক এক রকম। যস্মিন দেশে যদাচার— গোছের আর কী! কোথাও সূর্য কোথাও চন্দ্র, কোথাও সাপ, কোথাও খরগোশ, কোথাও চিল—কত রকম পশুপাখি দিয়ে হিসেব হয়। যে যার নিজের রেওয়াজ মতন ভূত-ভবিষ্যৎ বিচার করে। চুনি তো দাদার মুখ দেখেই একটা হিসেব করে নিল। তারপর…”
“হিসেবটা ভুলও হতে পারে।”
“পারে! ভগবানেরও হিসেব ভুল হয়। তবে চুনি ফেলনা নয় বউদি, ওর পাওয়ার আছে।’’
নবতারা একবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে কী দেখলেন তারপর নন্দর দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। ‘‘আপনার কী মনে হয়?”
নন্দ চায়ের কাপ তুলে নিয়েছিলেন। বললেন, “বউদি, মানুষ তার ভাগ্য জানে না। আমিই কী জানতাম। যে মানুষ সারাদিন সংসারের কাজকর্ম করল, সন্ধেবেলায় সেজেগুজে গিয়ে সিনেমা দেখে এল, সেই মানুষ খেয়েদেয়ে শুতে এসে বিছানায় বসল, কী চলে গেল! বলুন এর কোনও কারণ আছে! মানে পাবেন! তবু বলি ভুল সকলেরই হয়। চুনিরও হতে পারে। মহেশদাকে আমি সে কথা বলেছি। বলেছি—এটা মাথায় তোলা থাক। আপনি ও নিয়ে বেশি ভাববেন না। জন্মিলে মরিতে হবে—অমর কে কোথা কবে! বরং কী হবে সেটা ভুলে গিয়ে এই বেলায় বাকি কাজগুলো সেরে ফেলুন। হাতে এখনও সময় আছে।”
মহেশ বড় করে নিশ্বাস ফেললেন। বললেন, “নন্দ, বাকি কাজ তো ভাই অনেক ছিল, সব তো মেটাতে পারব না। সময় হবে না। অন্তত মেয়েটার বিয়েটা যদি চুকিয়ে দিতে পারতাম।”
“দিন না, আর দেরি করছেন কেন! বিনুমা আমাদের কী সুন্দর দেখতে। অমন গড়ন বাঙালি ঘরে ক’টা থাকে। ছিপছিপে লম্বা, মিষ্টি মুখ। গায়ের রংও ফেলনা নয়। ভীষণ ঝরঝরে, লেখাপড়াও শিখেছে। বয়েস কত হল—?”
“বাইশে পড়েছে।’’
“তবে আর কী! রাইট টাইম।”
মহেশ বললেন, “তা ঠিক। আমাদের সময়ে তো আঠারো কুড়িতেই হয়ে যেত।”
নবতারা বললেন, “চেষ্টা তো করছি ঠাকুরপো! ভাল ছেলে পাচ্ছি কোথায়? আপনাকেও তো কতবার বলেছি। ভাইঝির জন্যে একটা ভাল ছেলে জোগাড় করে দিন।”
“তা বলেছেন,” নন্দ সায় জানালেন। তারপর কী ভেবে বললেন, “দু একজনকে তো আপনারা দেখেছেন শুনেছি।”
“খোঁজ খবর করেছি, চোখে দেখেছি দু একজনকে,” নবতারা বললেন, “সেগুলো ছেলে নয়, ছাগল।’’
মহেশ চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে সিগারেট খুঁজতে লাগলেন পকেটে। নন্দর সঙ্গে একবার চোখ চাওয়া-চাওয়ি হয়ে গেল।
নন্দ চা খেতে খেতে কপাল চুলকে নিয়ে শেষে বললেন, “বউদি। একটা কথা বলি, কিছু মনে করবেন না। দাদা একশো বছর বাঁচুন, চুনির কথা মিথ্যে হোক। তবু কথাটা আপনাকে না বলে পারছি না। সাতটা দাদার কেটে যাবে, আট থেকে দাদার বড় একটা ভাল থাকার কথা নয়। স্ট্রোকট্রোক হতে পারে। চিনুর ফোরকাস্ট। ওই সময় বাকিটা—মানে বাকি ক’মাস—ক্রাইসিস পিরিয়ড…। সবই ভাগ্যের ব্যাপার বউদি। হয়তো কিছুই হল না, আবার হতেও পারে। আমার মনে হয় অত দেরি না করে খানিকটা আগে ভাগে যদি বিনুর বিয়েটা সেরে রাখতে পারেন—মেয়ের চিন্তাটা দূর হবে মহেশদার। তা ছাড়া বিয়ে তো দিতেই হবে। না কি মহেশদা?”
মহেশ বড় করে নিশ্বাস ফেললেন আবার। “আমার তো তাই ইচ্ছে। তবে মনের ইচ্ছে কি সব সময় মেটে হে! মেয়ের বিয়ে আর ছোট ছেলেটার চাকরি পাকা হয়ে গেলে ইচ্ছে ছিল তোমার বউদিকে নিয়ে দু একমাস হরিদ্বার দেরাদুন দিল্লি কাটিয়ে কাশি হয়ে ফিরব।”
নবতারা হঠাৎ নন্দকে বললেন, “আপনার ভাইকে একদিন এখানে আনুন না। আমাদের দেখে একবার বলুক না কী হবে! বিনুকে দেখে বলুক—বিয়েটিয়ে কবে আছে কপালে?”
নন্দ তাকালেন নবতারার দিকে। পরে বললেন, “চুনি দিন দুই চার পরে ফিরবে। ও আজ সকালে এক জায়গায় গেল। ফিরলে নিয়ে আসব।”
“আনুন। বেলাবেলি আনবেন। না হয় এখানেই খাওয়া-দাওয়া করবে একটা বেলা।”
“ও কিন্তু দিনের বেলা বেরুতে চায় না। সন্ধে করেই আনব।”
“তাই আনুন।”
নবতারা আর বসলেন না, উঠে পড়লেন।
মহেশ আর নন্দ সিগারেট শেষ করলেন, আর-একটা করে। বৃষ্টি থেমে আসার মতন হচ্ছিল।
ছাতা ছিল নন্দর কাছে। বললেন, “ওঠা যাক মহেশদা!”
“হ্যাঁ, চলো।”
নন্দকে নিয়ে মহেশ সদর পর্যন্ত আসতেই দরজার কাছে বিনুর সঙ্গে দেখা।
“নন্দকাকা! তুমি কখন এসেছ!”
“অনেকক্ষণ। কোথায় ছিলি তুই?”
“বাড়ি ছিলাম না। এই মাত্র ফিরলাম। … দেখো না, রিকশা থেকে নামতে গিয়ে শাড়ি ফাঁসল, বাঁ পাটাও গোড়ালির কাছে মচকে গেল। আমাদের গলির এখানটায় যা পেছল হয়।”
নন্দ হেসে বললেন, “তাই দেখছি।…আজ তা হলে বউদির কাছে—।।” “মা! ওরে বাব্বা। জানতে পারলে রক্ষে রাখবে না।”
“পালা তা হলে।”
বাইরে এসে মহেশ বললেন, “নন্দ, যে নদীতে কুমির থাকে—সেই জলে ঝাঁপ দিচ্ছি আমরা। এরপর—’’
নন্দ বলল, “ভেবে লাভ নেই দাদা। হয় মক্কা, না হয় ফক্কা।”
রাত্রে শুতে এসে নবতারা বললেন, “শুনছ তো!”
মহেশ জেগে ছিলেন। খোলা জানলা দিয়ে বর্ষার জলো বাতাস আসছিল। গুমোট গরম নেই। পাখাও চলছে। তবু ঘুমিয়ে পড়তে পারেননি। না পারার কারণ নবতারা। স্ত্রী বলে রেখেছিলেন, বিছানায় পড়লাম আর ঘুমোলাম না হয়, কথা আছে। তা ছাড়া মহেশ নিজেই খানিকটা চিন্তায় ছিলেন।
মহেশ সামান্য দেরি করে সাড়া দিলেন। “বলো।”
নবতারা তখনও বিছানায় শোননি, শাড়ি জামা আলগা করে মাথার খোঁপা সরিয়ে নিচ্ছিলেন ঘাড়ের কাছ থেকে। বললেন, “মেয়ের বিয়ে নিয়ে তোমার বড় চিন্তা।”
মহেশ ব্যাপারটা ধরতে পারলেন। সন্ধেবেলার কথার জের। বললেন, “কার না হয়। সব মা বাপেরই হয়ে থাকে।’’
“তা হলে ব্যবস্থা দেখো।”
“কী ব্যবস্থা দেখব।”
“ছেলে খোঁজো।”
“তুমিই খোঁজো না।”
“কেন! তুমি বাপ না! বাড়ির কর্তা, পুরুষ মানুষ। চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছ। কত চেনা শোনা।”
“আমায় আর খুঁজতে বোলো না। যে ক’টা খুঁজে বার করেছি—সব কটাকে তোমরা অপছন্দ করেছ।”
নবতারা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন স্বামীকে। বললেন, “ওকে খোঁজা বলে না। ছেলে কি মাঠে-চরা গোরু ছাগল যে গলায় দড়ি বেঁধে একটা ধরে আনলে আর হয়ে গেল। আমার বাবাকে দেখেছি..”
“তোমার বাবা কী জিনিস ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন তা তুমিই জান। তবে আমি যাদের খোঁজ দিয়েছিলাম—’’
“অখাদ্য। ওরা আবার ছেলে! আমার পছন্দ হয়নি, তোমারও বা হয়েছিল কোথায়! মেয়েরও নয়।”
“মেয়ের কথা তুমি জানলে কেমন করে?”
“আমি মা হয়ে জানব না, তুমি বাবা হয়ে জানবে! তোমার মতন বাপের কোনও মান-মর্যাদা আছে। ছেলেমেয়ের সঙ্গে হাসি ফক্কুড়ি করছ। বাপ না ইয়ার বোঝা যায় না। মেয়ে তো সবসময় বাপের সঙ্গে হ্যা হ্যা হিহি করছে। আমরা বাপু বাপকে যত ভালবাসতাম, তত ভয় পেতাম। তোমায় তো ওরা গ্রাহই করে না, ভাবে প্রাণের ইয়ার। দেখলে আমার গা জ্বলে যায়।”
মহেশ বললেন, “তোমার বাবার সঙ্গে আমাকে মেলাতে যেও না। তিনি তিনি, আমি আমি। …তুমি বলছ, আগে যাদের খোঁজ এনেছি মেয়েরও তাদের পছন্দ হয়নি।”
“হ্যাঁ।”
“আমি যদি বলি, একটা ছেলেকে পছন্দ ছিল।”
সঙ্গে সঙ্গে নবতারা একেবারে ঘুরে বসলেন? “কে? কাকে পছন্দ ওই নাচিয়ে ছেলেটাকে?”
“নাচিয়ে মানে! ও…”
“ও-টো রাখো। ওকে আমি দেখিনি নাকি! ভটভটি করে ঘুরে বেড়ায় এপাড়া ওপাড়া, মেয়েদের মতন লম্বা চুল মাথায়, চোখে ঠুলি, পোশাক আশাকের কী বাহার, যেন সং; সারা জামা প্যান্টে তাপ্পাতুল্পি, রং। ওটাকে আমি নাচতে দেখেছি। গত বচ্ছর এখানে যে ফাংশান হল তাতে পিঠ কোমর ভেঙে মাটিতে শুয়ে বসে কী নাচ। সেই সঙ্গে ঝমঝমা বাজনা। নাচ আর থামে না। হিন্দি সিনেমা। অখাদ্য। ছিছি, দামড়া একটা ছেলের ওই ঢং দেখে পিত্তি জ্বলে গেল! ওই হারামজাদা আবার ছেলে হল নাকি? ওকে তুমি নিজের মেয়ের পাত্র হিসেবে ভাবতে পারলে। রাম রাম।”
মহেশ সবই জানেন। বললেন, “তুমি শুধু নাচ দেখছ।”
“আবার কী দেখব! আমি ওকে নাচতে দেখেছি।”
“ইয়ে, মানে ওকে বলে ব্রেক ড্যান্স। আমি তো তাই শুনেছি। ব্রেক ড্যান্সের এখন খুব কদর। মডার্ন ক্রেজ। ওই নাচ ওই রকমই। শরীর ভেঙে ভেঙে নাচতে হয়। তা নাচটা ও জানে, শিখেছে। নাচে বলেই ছেলে খারাপ হবে। ও কম্পুটার এনজিনিয়ার, ভাল কাজকর্ম করে, বাপের ঘরবাড়ি আছে, বাবা রেলের বড় অফিসার ছিলেন। ভাল ফ্যামিলি।… আমাদের নন্দর সঙ্গে একটা রিলেশান আছে।’’
নবতারা ধমকে উঠে বললেন, “চুলোয় যাক তোমার ভাল ফ্যামিলি। বোম্বাইঅলাদের মতন দেখতে, —সাজ পোশাক, কুচ্ছিত নাচ, ভটভটি চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারাদিন, গুণ্ডা বদমাশের মতন—, ওর সঙ্গে ভদ্রলোক মেয়ের বিয়ে দেয়। একটা মাত্র মেয়ে আমাদের, আমি দেখেশুনে একটা বাঁদরকে জামাই করব! ছি, তোমার লজ্জা করল না বলতে।”
মহেশ চুপ। মাস কয়েক আগেও এক দফা তাঁকে এসব শুনতে হয়েছে।
হঠাৎ নবতারা বললেন, “কী বলছিলে তুমি? ওই বাঁদরকে বিনুর পছন্দ?”
মহেশ বিপদে পড়ে গেলেন। ঢোঁক গিলে কোনও রকমে বললেন “না—মানে, মনে হল অপছন্দ নয়।”
‘মনে হওয়াচ্ছি। দেখি তার কেমন পছন্দ।”
মহেশ তাড়াতাড়ি বললেন, “একটা কথা বললুম আর তোমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। দাঁড়াও না। মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে চাও দু-দিন পরেই বলবে।”
নবতারা আর কথা বললেন না।
তিন
দিন চারেক পর নন্দলাল এলেন। ঝাঁপিয়ে বৃষ্টি নেমেছিল বিকেলে, সন্ধের গোড়ায় থামল।
সন্ধেবেলায় গায়ে বর্ষাতি, মাথায় ছাতা নন্দলাল এলেন তাঁর ভাই চুনিকে নিয়ে। কথা ছিল আসার।
বসার ঘরে ঢোকার আগেই নন্দলাল উচু গলায় হাঁক মেরে বললেন, “বউদি, আজই আসতে হল বৃষ্টি বাদলার মধ্যে। চুনি কাল সকালেই দিল্লি মেলে চলে যাচ্ছে। আবার কবে আসবে ঠিক নেই। নিয়ে এলাম আজই।”
মহেশ কেমন চোরের মতন বললেন, “এসো। এসো।” বলেই নন্দকে চোখ টিপলেন। নিচু গলায় বললেন, “দিল্লি মেল রাত্রে পাস করে। মুখ্যু।”
নন্দ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, “ডাউন ট্রেন ভীষণ লেট যাচ্ছে ক’দিন।”
“এসো।”
বসার ঘরে বসলেন নন্দরা।
নন্দর ভাই চুনি—মানে তিব্বতি বাবার পোশাক খানিকটা পাল্টেছে যেন। একরঙা আলখাল্লা। টকটকে লাল। মাথায় কানঢাকা টুপি। ঘাড়ের পাশে চুল ঝুলছে। দাড়ি গোঁফ যথারীতি। চোখে রঙিন কাচের চশমা। পাতলা কাচ, রংটাও ফিকে। হাতে একটা ঝোলা।
মহেশ বার কয়েক নন্দকে কী বলব কী বলব করে শেষে বললেন, “ডাকি তা হলে!”
“হ্যাঁ, ডাকুন।…বিনুকেও তো আসতে হবে একবার। তা ও খানিকটা পরে এলেও হবে। বউদিকেই ডাকুন আগে।”
“বিনুটার ভীষণ সর্দি জ্বর। বৃষ্টিতে ভিজে জ্বর বাধিয়েছে। পায়েও ব্যথা। তবে আসবে। আজ জ্বর কমেছে।”
নন্দ বললেন, “চুনিরও গলা ভেঙে গেছে। কাল যে-গাড়িটা করে ফিরছিল সেটা রাস্তা থেকে হড়কে গিয়ে ডোবায় পড়ে গিয়েছিল। জলে কিছুক্ষণ হাবুডুবু খেয়েছে বেচারি।”
মহেশ বললেন, “জোর বেঁচে গেছে বলো। জলে হাবুডুবু বড় খারাপ। বসো, গিন্নিকে ডেকে আনি।”
খানিকটা পরে নবতারা এলেন।
মহেশ আগেই ফিরে এসেছিলেন, কথা বলছিলেন নন্দদের সঙ্গে।
নবতারা ঘরে আসতেই নন্দ পরিচয় করিয়ে দিলেন, “বউদি আজই আসতে হল। বৃষ্টি বাদলা মাথায় নিয়ে। চুনি কাল সকালেই চলে যাচ্ছে। মহেশদাকে আমি গতকালই বলে রেখেছিলাম—আজ আসার চেষ্টা করব।”
নবতারা চুনিকে দেখছিলেন।
চোখ বুজে, সামান্য জিব বার করে মাথাটা নুইয়ে ছিল চুনি। দু কানে হাত রাখল কয়েক পলক। অভিবাদন জানাল বোধ হয়।
নবতারা নন্দকে বললেন, “এসে ভাল করেছেন। না এলে আর ওঁকে দেখতে পেতুন না। তা কাল উনি কোথায় যাচ্ছেন?”
“কলকাতা হয়ে শিলিগুড়ি দার্জিলিং।”
“এখানেই থাকেন।”
“এখন বছর খানেক।”
“ঘরবাড়ি কি এদিকেই কোথাও?”
“হ্যাঁ ; এই তো বীরভূমে। চুনি বরাবরই বাড়ি-ছাড়া। ঘুরে বেড়াত এদিক ওদিক। কাজকর্ম করত। ভাল লাগত না। ছেড়ে দিয়ে পালাত অন্য কোথাও। ওই করতে করতে তিব্বত চলে গেল। ওর বরাবরই খানিকটা সাধু সন্ন্যাসীর সঙ্গে মেলামেশা ছিল। ওই থেকে যা হয়—মন চলে গেল সাধনা টাধনার দিকে।”
নবতারা শুনলেন। তারপর বললেন, “তা উনি আপনার দাদার ব্যাপারে যা বলেছেন, তা কি ঠিক?”
এবার চুনি বলল, ভাঙা গলায়, “যা দেখেছি তাই বলেছি।’’
“কী দেখেছেন? কুষ্টি তো দেখেন নি।”
“আপনাদের এই হরস্কোপ আমি দেখি না। আমরা মুখ দেখি। মুখ দেখে বলি। মুখের হিসেব আছে। তারপর অঙ্ক। অঙ্কের গোলমাল হতে পারে।”
“এক থেকে দশের পর আরও আছে?”
“আঠারো পর্যন্ত আছে।”
“ওনার হিসেব..”
“বিলকুল ঠিক। হিসেব ভুল হবে না। তবে ওপরঅলা যা করবেন।”
নবতারা নিজের মুখটা দেখালেন। “আমার মুখ দেখে কিছু বলুন।’’
চুনি একটু চুপ করে থেকে বলল, “আমি একটা মুখই দেখব। আপনার মুখ দেখলে আপনারই দেখব। মেয়ের মুখ দেখব না।’’।
নন্দ তাড়াতাড়ি বললেন, “বউদি আমি চুনিকে বলেছি, বিনুর মুখ দেখে দু চারটে কথা বলতে হবে।”
নবতারা বললেন, “দুটো মুখ দেখা যায় না।”
চুনি বলল, “আমি দেখি না। কাগজ পেনসিল দিন আপনারটাই হিসেব করি।”
মহেশ তাড়াতাড়ি বললেন, “তুমি কেন। বিনুকেই দেখুক না।”
নবতারা যেন কানই করলেন না, বললেন, “আমারটাই হোক। তোমার তো মন্দ শুনলাম। কতটা মন্দ আমাকে দিয়েই বোঝা যাবে। আমার ভাগ্যেও যদি খারাপ থাকে—!”
সাদামাটা যুক্তি। স্বামীর ভাগ্যের অন্তত খানিকটা স্ত্রীর ভাগ্যেও বর্তাবে।
মহেশকে বাধ্য হয়ে কাগজ কলম জুগিয়ে দিতে হল।
চুনি তার হালকা রঙিন কাচের চশমার আড়াল থেকে নবতারাকে দেখল বার বার, তারপর কাগজ কলম নিয়ে হিসেবে বসল। লাইন টানল নানা রকম, ছোট বড়, কাটাকুটি করল, চৌকো গোল নানান ছাঁদের চেহারা এল এখানে সেখানে। শেষে অঙ্ক। যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ—হয়ত জ্যামিতির অঙ্কও হল।
অতক্ষণ ধৈর্য ধরে বসে থাকা মুশকিল। মহেশ একবার বাইরে গেলেন, ফিরে এলেন খানিকটা পরে। নন্দ হাই তুলতে লাগলেন। দু চারটে কথাও হল মহেশের সঙ্গে নিচু গলায়। বাইরে মেঘ ডাকছে। বৃষ্টি আবার আসতেও পারে।
নবতারা কিন্তু একই ভাবে বসে বসে চুনিকে দেখছিলেন। দু চার বার চোখ সরে যাচ্ছিল স্বামীর দিকে।
শেষ পর্যন্ত নন্দ বললেন ভাইকে, “কিরে? হল?”
চুনি মাথা হেলাল। বড়সড় নিশ্বাস ফেলে বলল, “হয়েছে।” “কী হল?”
“অবিন্ধন দশা।”
“মানে?”
‘তেরো চোদ্দ পনেরোর কাউন্ট। অহি হল সাপ। স্নেক। সাপের বন্ধন। মানে সংসারের দড়াদড়ি দুশ্চিন্তা ভাবনায় একেবারে জড়িয়ে পড়বেন। না, ওদিকে কোনও ভয় নেই, দেহহানি ঘটবে না। তবে মন আর এখনকার মতন থাকবে না। সুখশাস্তি যা পাবার, পাওয়া হয়ে গিয়েছে। আবার খানিকটা পাবেন পনেরোর ঘরে। তা, সে পেতে পেতে বছর দশ। ওটাই শেষ।”
নবতারা বললেন, “এতকাল তবে সুখশান্তি পেয়েছি।”
“আমার হিসেব বলছে।”
“বললেই আমায় মানতে হবে। সুখ যে কত পেয়েছি আর শান্তিতে কেমন আছি—আমিই জানি। তা যাক গে সেকথা। আমার ভাগ্যেও তা হলে ওঁর কোনও আপদ কাটল না।”
“না, তেমন কিছু দেখছি না।”
এমন সময় বিনু এল। বিনুর সঙ্গে এ-বাড়ির কাজের মেয়েটা, ফুলু। ট্রে সাজিয়ে চা খাবারটাবার এনেছে। বিনু সামান্য খোঁড়াচ্ছিল। একটা পায়ের গোড়ালিতে ক্রেপ ব্যান্ডেজ জড়াননা। মচকানো পা।
বিনু মেয়েটি দেখতে বেশ। ছিপছিপে গড়ন, মিষ্টি মুখশ্রী, চোখ দুটি হাসভিরা, থুতনির মাঝখানে ছোট্ট মতন গর্ত। চমৎকার ঝরঝরে মেয়ে।
বিনু নিচু হয়ে চা খাবার এগিয়ে দিচ্ছিল নন্দদের।
নন্দ চুনিকে বললেন, “চুনি, এ আমাদের বিনুমা।” বলে হাসিমুখেই বিনুকে বললেন, “কিগো সেই পায়ের চোট। এখনও খোঁড়াচ্ছ।”
“মচকে গিয়েছে। যা ব্যথা!”
“ভাঙেনি তো?”
“ভাঙলে দাঁড়াতে পারতাম নাকি?”
মাথা নাড়লেন নন্দ। “তা ঠিক।” বলতে বলতে চুনির দিকে তাকালেন আবার, “চুনি—একবার না হয় তোমার নিয়মটা ভাঙলে। বিনুমায়ের এটা যদি একবার দেখতে।”
চুনি কিছুই বলল না। বিনুকে দেখতে লাগল।
নবতারা বললেন, “না, না, জোরাজুরি করে লাভ নেই। ওঁর যখন নিয়ম নেই তখন আর কেন…”
নবতারার কথা শেষ হল না, চুনি বলল, “ওকে বসতে হবে না। আমার দেখা হয়ে গেছে। তুমি যেতে পারো। তোমার পুরো নামটা কী?”
“বিনতা।”
“বি-ন-তা! ঠিক আছে তুমি যাও।”
বিনু চলে গেল।
চা খাবার খেতে খেতে নন্দ বললেন, “মেয়েটাকে একটু ভাল করে দেখলে না চুনি।’’
“দেখেছি।”
“দেখেছ। ওই দেখাতেই হবে! তা একবার…”
“কোনও দরকার নেই নন্দদা। মেয়েটির অনেক সুলক্ষণ আছে। বয়েস কত। “কুড়ি পেরিয়েছে?”
“বাইশ,” মহেশ বললেন।
“তা হলে তো বেশ ভাল! কুড়ির পর থেকেই শঙ্খ।”
‘‘শঙ্খ।’’
“দরং টংলা। কুমুদহি গজাধী শঃ। ওসব আপনাদের বোঝার কথা নয়। এ মেয়ে পরম ভাগ্যবতী। বাপমায়ের সংসারের অনেক ভাল করেছে।”
মহেশ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, “তা ঠিক। বিনুর জন্মের পর থেকেই আমার উন্নতি।” বলে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। “আমাদের অনেক ঝঞ্জাট কেটে গিয়েছে—তাই না।”
নবতারা কিছুই বললেন না।
চুনি বলল, “ও হল চার পাঁচ ছয়ের কাউন্ট। বিষ্ণু শঙ্খ। স্বর্ণ শ্বেতাভ। সুখ। আনন্দ সম্পদ বৃদ্ধি করে। ভাগ্যবতী।”
নন্দ বললেন, “বিয়ের কোনও যোগটোগ নেই?”
“যোগ হয়ে গেছে নন্দদা! বিয়ে সামনেই।”
“যোগ হয়ে গেছে! পাত্র! পাত্রের কথা কিছু বলতে পার?”
চুনি মাছের চপ খেতে খেতে বলল, “সাউথ ইস্ট!”।
“সাউথ ইস্ট মানে? সে তো রেলওয়ে—সাউথ ইস্টার্ন!”
“রেল নয়। সাউথ ইস্ট ডিরেকশন থেকে পাত্র আসবে।”
“সাউথ ইস্ট! সে তো গোটা…”
“না না, খুব দূর হবার কথা নয়। কাছাকাছি থেকেই।”
“ছেলে কেমন হবে? কী করবে টরবে?”
“ছেলে ভালই হবে। হেলদি, লেখাপড়া জানা। চোখ হয়তো একটু কটা হবে। দেখবেন—মিশুকে হবে খুব!”
“কাজকর্ম?” মহেশ বললেন।
“ভাবতে হবে না। কালে নাকালে লক্ষ…”
“লক্ষপতি?”
“না না কালে কালে অনেক করবে।”
নবতারা এবার কথা বললেন। “মেয়ের ভাগ্যে তার বাবার ওই মন্দটা কেটে যেতে পরে না?”
চুনি কী ভাবল। চোখ বন্ধ করে হয়তো হিসেব করল কিছু। তারপর বলল, “ঠিক। কাটতে পারে। আপনি ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন বউদি। মেয়ে আপনার পারে। তবে ওর ভাগ্যটা আরও একটু পোক্ত করিয়ে দেবেন।”
“কেমন করে?”
“বিয়েটা দিয়ে দেবেন আগে। বিয়ে হলে যুগ্ম হয়।”
“ইচ্ছে তো খুবই—”
“ইচ্ছে বলবতী হলে সবই হয়। আপনারা অনর্থক সময় নষ্ট করবেন না। শুভ কাজ যত তাড়াতাড়ি পারা যায় সেরে ফেলা ভাল। তা ছাড়া মহেশদার সময়টা মনে রাখবেন।”
নবতারা মাথা হেলিয়ে জানালেন, তাঁর মনে থাকবে।
চার
মহেশের ঘুম এসে গিয়েছিল, গা-নাড়া খেয়ে ঘুম কাটল। চোখ খুলে তাকালেন। দেখলেন নবতার পাশে বসে আছেন। আতঙ্কিত হলেন।
“কী হল?” মহেশ বললেন।
“ওঠো। উঠে বসো।”
“কেন! উঠে বসার কী হল?”
“দরকার আছে!”
মহেশ বললেন, “শুয়ে শুয়ে হয় না?”
“ওঠো।”
মহেশ উঠে বসলেন।
নবতারা বললেন, “তুমি এত বড় জোচ্চোর, আমি জানতাম না।”
“ঠগ! জোচ্চোর! কী বলছ?”
“ন্যাকামি কোরো না। আমি কচি খুকি নয়, হাঁদাবোকা মুখও নয়। তুমি আমার সঙ্গে চিটিংবাজি করলে?”
মহেশ রীতিমতন ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। বললেন, “আমি আবার কী করলুম।”
“যা করেছ তুমি জান! ন্যাকা সাজতে এসো না।.. তুমি মেয়ের হয়ে গল্প ফেঁদে আমায় বোকা বানাবার চেষ্টা করলে!… ওই চুনিটা কে? মিথ্যে বলবে না। আমি সব জানি। ছেলেকে দিয়ে বলিয়ে নিয়েছি।”
মহেশ বুঝতে পারলেন, জলের কুমির তাঁকে ধরেছে। পালাবার পথ নেই। নন্দ তাঁকে কুমিরের মুখেই ঠেলে দিল।
মহেশ বললেন—“চুনি—মানে চুনি হল নন্দর মামাতো ভাই।”
“আর ওই নাচিয়ে ছেলেটা?”
“চুনির মাসতুতো দাদা।”
“বাঃ! মামাতো মাসতুতো! দড়ি বাঁধাবাঁধি।
“এসব বুদ্ধি কে দিয়েছিল?”
“নন্দ আর চুনি। নন্দই আসল।”
“ওরা পরামর্শ দিল, আর তুমি নিলে?”
মহেশ একটু চুপ করে থেকে বললেন, “কী করব! মেয়েটা যে ওই বাচ্চু ছেলেটাকেই পছন্দ করে। লাভ করে। প্রেম।”।
“তোমায় বলেছে।”
“বাঃ, বলবে না!”
“তোমারই তো মেয়ে! আর ওই নাচিয়েটা?”
“আরে বাবা, সে তো আমাদের মাথা খেয়ে ফেলল।”
নবতারা একটু চুপ করে থেকে বললেন, “তা হলে আর কী! এবার মেয়েকে বলো একটা পাঁজি আনতে। বাপেতে-মেয়েতে মিলে দিন ঠিক করে নাও।”
মহেশ বড় অস্বস্তিতে পড়লেন। কী যে বলেন। শেষে বললেন, “পাঁজি তো তুমি দেখবে!”
“না !”
“না কেন?”
“পছন্দ তোমাদের, ভালবাসা তোমাদের, আহ্লাদ তোমাদের—তোমরাই যা করার করবে। এই বিয়েতে আমি নেই। বিয়ের সময় আমি থাকবও না এখানে। বেনারসে দিদির কাছে চলে যাব।”
মহেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, “তুমি বড় জেদ করছ! তুমি বুঝতে পারছ না, আজকালকার ছেলেমেয়েদের ধাত আলাদা। তারা তাদের মতন পছন্দ করে, ভাবে, নিজেদের ভালমন্দ নিজেরাই ঠিক করে নেয়। বিনু ওই বাচ্চু ছেলেটাকে সত্যিই ভালবাসে। আমি তোমার ছোট ছেলেকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলল, বাবা, গো অ্যাহেড! আমরা সব জানি। দারুণ হবে।”
“হোক দারুণ। আমায় বাদ দিয়ে দারুণ হোক।”
মহেশ বললেন, “তোমাকে বাদ দিয়ে আমরা! বলছ কী?”
“ঠিক বলছি। মেয়ের ভালবাসা দেখে তোমার প্রাণ হু হু করে উঠল—তার হয়ে নাচতে নামলে, আর আমি যে চল্লিশটি বছর তোমার সব কিছু আগলে রাখলুম—আমার মান-মর্যাদাটুকু রাখলে না। এই রকমই হয়! আমাকে তোমরা তুচ্ছ করলে। ঠিক আছে। তোমাদের পাঁঠা তোমরা যেখানে খুশি কাটো।”
মহেশ হঠাৎ স্ত্রীর কোলের ওপর মুখ থুবড়ে পড়লেন। পড়েই বললেন, “আমি তো তোমারই পাঁঠা। তুমি রাখলে আছি, নয়ত’ নেই। ঠিক আছে, মেয়েকে বলে দেব, বাচ্ছু হবে না।”
নবতারা স্বামীর মাথা কোল থেকে সরিয়ে দিলেন। বললেন, “আমি বলে দিয়েছি আজই।”
“সর্বনাশ! কী বলেছ?”
“বলেছি, যা তুই ওই ছোঁড়াটাকে বিয়ে করগে যা! তোর বাপ যখন বলছে, ছেলে ভাল তখন ভাল। আমি আর কিছু জানি না।”
মহেশ মহানন্দে স্ত্রীর গালে গাল ঘষে বললেন, “এই না হলে তুমি আমার তারাসুন্দরী। আহা, এমন মা ক’টা ছেলেমেয়েই বা পায়।”
নবতারা বললেন, “আদিখ্যেতা কোরো না। রসাতল কাকে বলে এবার তুমি দেখবে।”
হৃদয় বিনিময়
আজ পাঁচ সাত বছর হয়ে গেল বটকৃষ্ণ পুজোর মুখে দেওঘরে চলে আসছেন। জায়গাটা তাঁর খুবই পছন্দ হয়ে গিয়েছে, স্ত্রী নলিনীরও। এখানকার জল-বাতাসে নলিনীর শ্বাসের কষ্ট কম হয়, বাতের ব্যথাটাও সহ্যের মধ্যে থাকে। বটকৃষ্ণর নিজেরও খুচরো আধিব্যাধি বেশ ঢাপা পড়ে এখানে। দেওঘরে পাকাপাকিভাবে থাকার একটা ইচ্ছে বটকৃষ্ণের মনে মনে রয়েছে। ছেলেমেয়েদের জন্যে হয়ে উঠছে না, তারা দেওঘরের নাম শুনলেই নাক মুখ কোঁচকায়। প্রথম প্রথম এক-আধবার ছেলেমেয়েরা বটকৃষ্ণর সঙ্গে এসেছিল, এখন আর আসতে চায় না, বড় ছেলে বন্ধুবান্ধব নিয়ে নৈনিতাল মুশৌরি রানীক্ষেত করতে যায়, ছোট পালায় পাহাড়ে-চড়া শিখতে, মেয়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে চিঠি লেখে ; ‘মা, তোমার জামাই একেবারেই ছুটি পাচ্ছে না, পুজোয় আমরা কোথাও যাচ্ছি না।’
বটকৃষ্ণ অবশ্য কারও তোয়াক্কা তেমন করেন না। বাষট্টি পেরিয়ে গিয়েছেন, তবু নুয়ে পড়েননি; শরীর স্বাস্থ্য এ-বয়সে যতটা মজবুত থাকা দরকার তার চেয়ে এক চুল কম নেই। খান-দান, বেড়ান, নলিনীর সঙ্গে রঙ্গ-তামাশা করেন, শীতের মুখে ফিরে যান।
এবারে বটকৃষ্ণ ভায়রা সত্যপ্রসন্নকে আসতে লিখেছিলেন। একটা উদ্দেশ্য অবশ্য বটকৃষ্ণর ছিল। ইদানীং দু তিন বছর তিনি যে-বাড়িটায় উঠছেন—সেটা বিক্রি হয়ে যাবার কথা। বটকৃষ্ণর মনে মনে ইচ্ছে বাড়িটা কিনে ফেলেন। বাংলো ধরনের ছোট বাড়ি, কিছু গাছপালা রয়েছে ; পাশের দু চারখানা বাড়িও ভদ্রগোছের, পরিবেশটা ভাল।
সত্যপ্রসন্ন বটকৃষ্ণর নিজের ভায়রা নন, নলিনীর মাসতুতো বোন মমতার স্বামী। বয়েসে বছর ছয়েকের ছোট। পেশায় ছিলেন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। বটকৃষ্ণর ইচ্ছে সত্যপ্রসন্নকে দিয়ে বাড়িটা দেখিয়ে তার মতামত নেন, ভবিষ্যতে সামান্য কিছু অদল-বদল করতে হবে—তারই বা কি করা যায়—সে-পরামর্শও সেরে রাখেন। সত্যপ্রসন্ন মত দিলে—বটকৃষ্ণ বায়নটাও করে রাখবেন। সত্যপ্রসন্ন স্ত্রী মমতাকে নিয়ে দেওঘর এসেছেন গতকাল। তারপর পাক্কা ছত্রিশ ঘণ্টা কেটে গেছে।
সন্ধেবেলায় বাইরের দিকের ঢাকা বারান্দায় চারজনে বসেছিলেন ; বটকৃষ্ণ, নলিনী, সত্যপ্রসন্ন আর মমতা।
ভায়রার হাতে চুরুট গুঁজে দিয়ে বটকৃষ্ণ বললেন, “সত্য, তোমার ওপিনিয়ানটা কী?”
সত্যপ্রসন্ন চুরুট জিনিসটা পছন্দ করেন না। তবু ধীরে-সুস্থে চুরুট ধরিয়ে নিয়ে বললেন, “বাড়ি খারাপ নয়, একটা একস্ট্রা বাথরুম তৈরি করা, কিচেনটাকে বাড়ানো—এসব কোনো সমস্যাই নয়। কুয়োয় পাম্প বসিয়ে ছাদের ওপর ট্যাংকে জল তোলাও যাবে—কলটল, কমোড—কোনোটাতেই আটকাবে না। কিন্তু এত পয়সা খরচ করে এ-বাড়ি নিয়ে আপনি করবেন কী?”
বটকৃষ্ণ চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, “বাড়ি নিয়ে লোকে কী করে হে! আমরা থাকব।”
“পারবেন থাকতে বুড়োবুড়িতে?”
“না পারার কোনো কারণ দেখছ? ছেলেমেয়েরা এখন সাবালক; বেকার নয়, খোঁড়া অন্ধ মাথামোটা নয়, তাদের সংসার তারা করুক, আমরা বুড়োবুড়িতে এখানে থাকব।”
মমতা বললেন, “এখন মুখে বলছেন জামাইবাবু, সত্যি কি আর তাই পারবেন? নন্তুর বিয়ে দেননি এখনও। বাড়িতে বউ এলে দিদিই কি এখানে থাকতে পারবে?”
বটকৃষ্ণ বললেন, “ছেলের বউ বড়, না আমি বড়—সেটা তোমার দিদিকেই জিগ্যেস করো।”
সাদা মাথা, সাদা খোলের লাল চওড়া পেড়ে শাড়ি, গোলগাল—ফরসা, বেঁটেখাটো মানুষটি একপাশে বসেছিলেন। মাথার কাপড় ঠিক করে নলিনী বললেন, “ছেলের সঙ্গে রেষারেষি করছ নাকি?”
বটকৃষ্ণ জবাব দিলেন, “তোমার বাবার সঙ্গে করলাম—তা ছেলে।”
মমতা হেসে উঠলেন।
সত্যপ্রসন্ন একটু চুপচাপ থেকে খুঁতখুঁতে গলায় বললেন, “আপনার ওই পাশের বাড়ির ভাবগতিক আমার ভাল লাগছে না, দাদা। সারাদিন দেখছি দুটো ছোঁড়াছুঁড়িতে যা করছে—একবার দোলনায় দুলছে, একবার রবারের চাকা নিয়ে খেলছে, এ ছুটছে তো ও পেছন পেছন দৌড়চ্ছে। দুপুরবেলায় দেখলুম, ছুঁড়িটা আমতলায় জালের দোলনা বেঁধে শুয়ে শুয়ে নবেল পড়ছে—আর ছোঁড়াটা মাঝে মাঝে দোলনার নীচে বসে মেয়েটাকে ঢুঁ মারছে। নাচ, গান, হল্লা তো আছেই। এ যদি আপনার নেবার হয় জ্বলেপুড়ে মরবেন।”
বটকৃষ্ণ বললেন, “তুমি আইভির কথা বলছ। জি সেনের মেয়ে। আরে, ও তো আমার খুব পেট। ওই ছেলেটি হল, পঙ্কজ। ডাক্তারি পরীক্ষা দিয়ে বসে আছে। ভেরি ব্রাইট। আইভির সঙ্গে লভে পড়েছে। দুটোই মাঝে মাঝে আমাদের কাছে আসে, নলিনীকে নাচায়।”
সত্যপ্রসন্ন কেমন থতমত খেয়ে গেলেন। ঢোক গিলে বললেন, “আপনি কি বলছেন, দাদা? একে লাভ বলে? ছাগলের মতন দুটোতে গুঁতোগুঁতি করছে?”
বটকৃষ্ণ নিবন্ত চুরুটে অভ্যেসবশ টান দিয়ে বললেন, “গুঁতোগুঁতি তো অনেক ভাল। সত্য, তুমি ইঞ্জিনিয়ারিং বোঝ, কিন্তু ভগবানের এই কলকবজার কেরামতি কিছু বোঝ না। লভ হল আরথকোয়েক, বাসুকী কখন যে ফণা নাড়িয়ে দেয়, কিস্যু বোঝ যায় না।” বলে বটকৃষ্ণ চশমার ফাঁক দিয়ে নলিনীকে দেখলেন। রঙ্গরসের গলায় বলেন, “ও নলিনী, তোমার ভগিনিপোত ওই ছেলেমেয়ে দুটোর গুঁতোগুঁতি দেখছে। ওকে একেবার তোমার লভ করার গল্পটা শুনিয়ে দাও না। ব্যাপারটা বুঝুক।’
নলিনী অপ্রস্তুত। লজ্জা পেয়ে বললেন, “মুখে কিছু বাধে না। ভীমরতি। বুড়ো বয়সে আর রঙ্গ করতে হবে না।”
“বটকৃষ্ণ বললেন, “রঙ্গ করব না তো করব কি! তোমার সঙ্গে রঙ্গ করলাম বলেই না বত্রিশটা বছর সঙ্গ পেলাম।”
মমতা হেসে বললেন, “জামাইবাবুর কি বত্রিশ হয়ে গেল?’
“হ্যাঁ ভাই, বত্রিশ হয়ে গেল। ইচ্ছে ছিল গোল্ডেন জুবিলি করে যাব। অতটা দূরদর্শী হতে ভরসা পাচ্ছি না। গোল্ডেনের এখনও আঠারো বছর।”
মমতা বললেন, “ভগবান করেন আপনাদের গোল্ডেনও হোক। আমরা সবাই এসে লুচি-মণ্ডা খেয়ে যাব। কিন্তু এখন আপনার বিয়ের গল্পটা বলুন, শুনি।”
সত্যপ্রসন্নর ধাত একটু গম্ভীর। চুরুটটা আবার ধরিয়ে নিলেন।
বটকৃষ্ণ নলিনীকে বললেন, “তোমার নিতাই প্রভুকে ডাকো, একটু চা দিতে বলো।” বলে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। একটু পরে বললেন, “আহা, কী খাসাই লাগছে! সত্য, কেমন একটু শীত শীত পড়েছে দেখছ! এই হল হেমন্তকাল। দেবদারু গাছের গন্ধ পাচ্ছ তে! বাড়ির সামনে দুটো দেবদারু গাছ। তার মাথার ওপর দিয়ে তাকাও, ওই তারাটা জ্বলজ্বল করছে, সন্ধেতারা। এমন একটা বাড়ি কি ছেড়ে দেওয়া ভাল হবে, সত্য? কিনেই ফেলি—কি বলো? কিনে তোমার দিদিকে প্রেজেন্ট করে দি, বত্রিশ বছরের হৃদয়অর্ঘ্য!”
নলিনী তাঁর সোনার জল ধরানো গোল গোল চশমার ফাঁক দিয়ে স্বামীকে দেখতে দেখতে বললেন, “আমায় দিতে হবে না, তোমার জিনিস তোমারই থাক।”
বটকৃষ্ণ বললেন, “আমার তো তুমিই আছ। তুমি থাকতে আমার কিসের পরোয়া। তোমার অমন জাঁদরেল বাবা, আমার শ্বশুরমশাইকে পর্যন্ত আমি তোমার জোরে কবজা করে ফেললাম, আমার ভয়টা কিসের?”
মমতা হাসতে হাসতে উঠে দাঁড়ালেন, “আমি চায়ের কথা বলে আসছি। জামাইবাবু, আপনার বিয়ের গল্পটা কিন্তু আজ শুনব। শুনেছি, আপনি নাকি বিয়ের আগে অনেক কীর্তি করেছেন!”
নলিনী বললেন, “তুই আর ধুনোর গন্ধ দিস না বাপু, এমনিতেই তো মরছি—”।
বটকৃষ্ণ বললেন, “আমায় গন্ধ দিতে হয় না। আমি গন্ধমাদন।” সত্যপ্রসন্নও হেসে ফেললেন।
চা খেতে খেতে বটকৃষ্ণ মমতাকে বললেন, “আমার বিয়ের গল্পটা হালফিলের নয়, ভাই। তোমার কত বয়েস হল, পঞ্চাশ-টঞ্চাশ বড় জোর। তুমি খানিকটা বুঝবে। আমার যখন পঁচিশ বছর বয়েস—তখন অষ্টম এডওয়ার্ড প্রেমের জন্যে রাজত্বই ছেড়ে দিলেন। ব্যাপারটা বোঝ, এত বড় ব্রিটিশ রাজত্ব—যেখানে কথায় বলে সূর্যাস্ত হয় না—সেই রাজত্ব প্রেমের জন্যে ছেড়ে দেওয়া। তখন প্রেম-ট্রেম ছিল এই রকমই পাকাপোক্ত ব্যাপার। তা আমি তখন একরকম ভ্যাগাবাণ্ডা। লেখাপড়া শিখে একবার রেল একবার ফরেস্ট অফিসে ধরনা দিয়ে বেড়াচ্ছি, কোথাও ঠিক ঢুঁ মেরে ঢুকতে পারছি না। আমার বাবা বলছেন, ল’ পড়। আমি বলছি—কভভি নেহি। মাঝে মাঝে ছেলে পড়াই। এই করতে করতে এসে পড়লাম আসানসোলে। একটা চাকরি জুটল, মাইনে চল্লিশ। সেখানে তোমার দিদিকে দেখলাম, বছর ষোলো সতেরো বয়েস, রায়সাহেব করুণাময় গুহর বাড়ির বাগানে কুমারী নলিনী গুহ একটা সাইকেল নিয়ে হাফ প্যাডেল মারছে, পড়ছে, উঠছে আবার পড়ছে। এখন হংসডিম্বর মতন তোনার যে দিদিটিকে দেখছ—তখন তিনি এইরকম ছিলেন না—কচি শসার মতন, লিকলিকে ফিনফিনে ছিলেন…।”
নলিনী কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করে বললেন, “তবু রক্ষে শসা বলেছ, ঢেঁড়শ বলোনি।”
মমতা হেসে উঠলেন। সত্যপ্রসন্ন চুরুটে আরাম পাচ্ছিলেন না। চুরুট ফেলে দিয়ে সিগারেট ধরালেন।
বটকৃষ্ট হাসতে হাসতে বললেন, “ঢেঁড়শ লম্বার দিকে বাড়ে, তুমি ও-দিকটায় পা বাড়ওনি। তা বলে তুমি কি দেখতে খারাপ ছিল। মাথায় একটু ইয়ে হলেও লিকলিকে লাউ ডগার মতন খুব তেজি ছিলে। নয়ত আমি যেদিন ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে তোমার সাইকেল থেকে পতন দেখলাম—সেদিন শাড়ি সামলে উঠে দাঁড়িয়ে আমায় জিবও ভেঙাতে না, হাত তুলে চড়ও দেখাতে না।”
মমতা হেলেদুলে খিলখিল করে হেসে উঠলেন। বয়েসে গলা মোটা হয়ে গিয়েছে—খিলখিল হাসিটা মোটা মোটা শোনাল। “দিদি, তুমি চড় দেখিয়েছিলে?”
নলিনী বললেন, “দেখাব না! লোকের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে অসভ্যতা করা। আবার দাঁত বের করে হাসা হচ্ছিল!”
“তা কি করব—” বটকৃষ্ণ চায়ের পেয়ালায় বড় করে চুমুক দিলেন। “তুমিই বলো মমতা, দাঁতটা যত সহজে বার করা যায়, হৃদয়টা তো তত সহজে বার করে দেখানো যায় না। যদি দেখানো যেত, আমি একেবারে সেই মুহূর্তে দেখিয়ে দিতাম—তোমার দিদি আমার হৃদয় ফাটিয়ে দিয়েছে।”
সত্যপ্রসন্নর মতন গম্ভীর মেজাজের লোকও এবারে হেসে ফেললেন। হয়ত মুখে চা থাকলে বিষম লেগে যেত। মমতাও হাসছিলেন।
বটকৃষ্ণ ধীরেসুস্থে তাঁর নিবন্ত চুরুট আবার ধরিয়ে নিলেন। বললেন, “প্রথম দর্শনে প্রেম—লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট যাকে বলে—আমার তাই হল। পা আর নড়তে চায় না। চক্ষু আর পলক ফেলে না। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়। এমন সময় রায়সাহেব করুণাময় গুহর বাড়ির এক নেড়ি কুত্তা ফটকের কাকলিনী যদি বুদ্ধিটা না দিতছে এসে চেল্লাতে লাগল। তার চেল্লানির চোটে বাড়ির লোক জমে যাবার অবস্থা। আমি আর দাঁড়ালাম না ভয়ে।”
নলিনী বললেন, “আমার বাবা নেড়ি কুকুর পোষার লোক নয়। ওটা খাস অ্যালসেশিয়ান। নাম ছিল কাইজার।”
বটকৃষ্ণ মিটমিটে চোখ করে বললেন, “খাস নেড়িও নয়, তাদের তেজও কম নয়। সে যাক গে, তখনকার মতন তো পালালাম। কিন্তু চোখের সামনে সেই কচি শসা দুলতে লাগল। কুকুরের মুখের ডগায় মাংস ঝুলিয়ে তাকে দৌড় কালে যেমন হয়—আমাকেও সেই রকম আড়াই মাইল দৌড় করিয়ে শসাটা বিছানায় ধপাস করে ফেলে দিল।”
সত্যপ্রসন্ন বললেন, “আড়াই মাইল কেন?”
বটকৃষ্ণ বললেন, “আড়াই মাইল দূরে একটা মেসে আমি থাকতাম। মেসে গিয়ে সেই যে শুলাম—আর উঠলাম না। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে গেল, সত্য। তোমার বড় শালী চোখের সামনে সাইকেল চড়তে লাগল। আর বার বার দেখতে লাগলাম সেই জিব ভেংচানো, চড় মারার ভঙ্গি। কালিদাস খুব বড় কবি, কিন্তু একবারও খেয়াল করলেন না, শকুন্তলা যদি খেলাচ্ছলে একবারও রাজা দুষ্মন্তকে চড় দেখাত কিংবা জিব ভেঙাত, কাব্যটা তবে আরও জমত।…আমার হল ভীষণ অবস্থা, সারাক্ষণ ওই একই ছবিটা দেখি। ঘুম গেল, খাওয়া গেল, অফিসের কাজকর্মও গেল। পাঁচের ঘরের নামটা ভুলে গিয়ে পাঁচ পাঁচচে পঁয়ত্রিশ লিখে ফেললুম হিসেবে। মুখুজ্যেবাবু বললেন, তোমাকে দিয়ে হবে না! …তা অত কথার দরকার কি ভাই, রোজনামচা লিখতে বসিনি। সোজা কথা, প্রেমে পড়ে গেলুম তোমার বড় শালীর। কিন্তু থাকি আড়াই মাইল দূরে, সাইকেল ঠেঙিয়ে প্রেমিকাকে দেখতে আসা বড় কথা নয়, বড় কথা হল—এলেই তো আর দেখতে পাব না। রায়সাহেব সশরীরে রয়েছেন, রয়েছে কাইজার, লোহার ফটক, বাড়ির লোকজন। তবু রোজ একটা করে গুড়ের বাতাসা মা কালীকে মানত করে রায়সাহেবের বাড়ির দিকে ছুটে আসতুম। এক আধ দিন দেখা হয়ে যেত, মানে দেখতুম—বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে প্রেমিকা আমার ধোপার সঙ্গে কথা বলছে, কিংবা বাগানে ঘুরে ঘুরে পাড়ার কোনো মেয়ের সঙ্গে হি-হি করছে। আমায় ও নজরই করত না।…আমার নাম বটকৃষ্ণ দত্ত। বটবৃক্ষের মতন আমার ধৈর্য, আর কৃষ্ণের মতন আমি প্রেমিক। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন করে লেগে থাকলুম আমি। শেষে একদিন, ‘কণ্ঠহার’ বলে একটা বায়োস্কোপ দেখতে গিয়ে চারি চক্ষুর মিলন এবং দুপক্ষেরই হাসি-হাসি মুখ হল। হাফ টাইমে বেরিয়ে স্যাট করে দু’ ঠোঙা চিনেবাদাম কিনে ফেললুম। অন্ধকারে ফিরে আসার সময় একটা ঠোঙা কোলে ফেলে দিয়ে এলুম শ্রীমতীর। লাভের ফার্স্ট চ্যাপ্টার শুরু হল।
মমতা পায়ের তলায় চায়ের কাপ নামিয়ে রাখলেন। হেসে হেসে মরে যাচ্ছেন বটকৃষ্ণর কথা শুনতে শুনতে। নলিনী আর কি বলবেন, ডিবের পান জরদা মুখে পুরে বসে আছেন।
বটকৃষ্ণ কয়েক মুহূর্ত সামনের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। বোধ হয় ফটকের সামনে দেবদারু গাছের মাথা ডিঙিয়ে তারা লক্ষ করলেন, তারপর গলা পরিষ্কার করে স্ত্রী এবং শালীর দিকে তাকিয়ে রঙ্গের স্বরে বললেন, “থিয়েটারে দেখেছ তো ফার্স্ট অ্যাক্টের পর সেকেন্ড অ্যাক্ট তাড়াতাড়ি জমে যায়। আমাদেরও হল তাই। নলিনী বিকেল পাঁচটায় চুল বাঁধতে বাঁধতে বারান্দায় এসে দাঁড়াত, কোনোদিন বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে থাকত, ফটকের সামনে এসে কুলপি মালাই ডাকত। আমি দুদ্দাড় দৌড়ে সময়মতন হাজির থাকতাম রাস্তার উল্টো দিকে। চোখে চোখে কথা হত, হাসি ছোড়াছুড়ি করে হৃদয় বিনিময়। রায়সাহেবের বাড়ির কম্পাউন্ডে ঢোকার সাহস আমার ছিল না। নলিনীরও সাধ্য ছিল না আমায় ভেতরে ডাকে। আজকাল ছেলেমেয়েরা কত সহজ—ফ্রি, লাভারের হাত ধরে বাপের কাছে নিয়ে যায়—বলে, আমার বন্ধু। বাবারাও আর রায়সাহেবের মতন হয় না। রায়সাহেব—মানে আমার ভূতপূর্ব শ্বশুরমশাই—ভূতপূর্ব বলছি এই জন্যে যে তিনি এখন বর্তমান নেই—যে কী জাঁদরেল মানুষ ছিলেন তোমরা জানো না। সেকেলে রেলের অফিসার। ফার্স্ট ওয়ারে নাকি লড়াইয়ে গিয়েছিলেন, বেঁটে চেহারা, রদ্দামারা ঘাড়, মাথার চুল কদম ছাঁট করা, তামাটে গায়ের রং, চোখ দুটো বাঘের মতন জ্বলত। গলার স্বর ছিল যেন বজ্রনিনাদ।”
নলিনী এবার ঝাপটা মেরে বললেন, “আমার বাবার নিন্দে কোরো না বলছি। যে মানুষ স্বর্গে গিয়েছেন তাঁকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা!”
হাত মাথা নেড়ে বটকৃষ্ণ বললেন, “নিন্দে কোথায় করছি, গুণগান গাইছি। আচ্ছা ভাই মমতা, তুমি ছেলেবেলায় এক-আধবার তোমার মেসোমশাইকে দেখেছ তো? আমি যা বলছি তা কি মিথ্যে! রায়সাহেব করুণাময়কে দেখলে কি মনে হত না গাদা বন্দুক তোমার দিকে তাক করে আছে। বাবারে বাবা, সে কি কড়া লোক, সাহেবি ডিসিপ্লিনে মানুষ—ফাজলামি করবে তাঁর সঙ্গে! চাকরি থেকে রিটায়ার করার পরও বড় বড় রেলের অফিসাররা খানাপিনায় তাঁকে ডাকত। আমি যখনকার কথা বলছি—তখন তিনি রিটায়ার করে গিয়েছেন, করে একটা ভাড়া করা বাড়ি নিয়ে থাকেন। প্রচণ্ড খাতির, লোকে ভয় পায় বাঘের মতন ; বলত কেঁদো বাঘ। সেই বাঘের বাড়িতে কোন সাহসে আমি ঢুকব বলো! এদিকে আমার যে হৃদয় যায় যায় করছে, রোজ অম্বল, চোঁয়া ঢেকুর ; ঘুম হয় না, খাওয়ায় রুচি নেই, দুঃস্বপ্ন দেখছি রোজ। শেষে তোমাদের ওই দিদি নলিনী একদিন ইশারা করে আমায় বাড়ির পেছন দিকে যেতে বলল।”
বাধা দিয়ে নলিনী বললেন, “মিথ্যে কথা বোলো না। আমি তোমায় কিছু বলিনি ; তুমিই একদিন একটুকরো কাগজে কী লিখে ছুড়ে দিয়ে পালিয়েছিলে!”
বটকৃষ্ণ বাধ্য ছেলের মতন অভিযোটা মেনে নিয়ে বললেন, “তা হতে পারে। একে বলে স্মৃতিভ্রংশ। বুড়ো হয়ে গিয়েছি তো?”
“সুবিধে বুঝে একবার বুড়ো হচ্ছ, আবার জোয়ান হচ্ছ।” নলিনী বললেন।
মমতা বললেন, “তারপর কী হল বলুন? বাড়ির পেছনে কী ছিল?”
বটকৃষ্ণ বললেন, “রায়সাহেবের বাড়ির পিছন দিকে ছিল ভাঙা পাঁচিল, কিছু গাছপালা—বাতাবিলেবু, কুল, কলকে ফুল এই সবের। খানিকটা ঝোপঝাড় ছিল। আর বাড়িঅলা সত্য সাঁইয়ের সে আমলের একটা ভাঙা লরি। লরির চাকা-টাকা ছিল না, পাথর আর ইটের ওপর ভাঙা লরিটা বসানো ছিল। আমরা সেই ভাঙা লরির ড্রাইভারের সিটে আমাদের কুঞ্জবন বানিয়ে ফেললাম। তোমায় কি বলব মমতা, যত রাজ্যের টিকটিকি গিরগিটি পোকা-মাকড় জায়গাটায় রাজত্ব বানিয়ে ফেলেছিল। দু-চারটে সাপখোপও যে আশেপাশে ঘোরাঘুরি না করত তা নয়। কিন্তু প্রেম যখন গনগন করছে তখন কে ও সবের তোয়াক্কা রাখে। ভয় তো সব দিকেই ছিল—রায়সাহেব করুণাময় একবার যদি ধরতে পারেন হান্টার চালিয়ে পিঠের চামড়া তুলে দেবেন, বিন্দুমাত্র করুণা করবেন না। তা ছাড়া রয়েছেন নলিনীর বোন যামিনী। আর এক যন্ত্রণা। ওদিকে ছিল কালু—বাচ্চা হলে হবে কি রাম বিচ্ছু। তার ওপর সেই নেড়ি কাইজার। রোজ চার ছ’আনার ডগ বিস্কুট নিয়ে যেতাম পকেটে করে। তাতেও ভয় যেত না। বিস্কুট খেলেই কুকুর মানুষ হয় না। বিপদে পড়তে পারি ভেবে বান রুটির মধ্যে আফিঙের ডেলা মিশিয়ে পকেটে রাখতাম।”
সত্যপ্রসন্ন আবার একটা সিগারেট ধরালেন। বললেন, “কুকুরকে আফিঙের নেশা করালেন? এরকম আগে কই শুনিনি।”
“শুনবে কোথা থেকে হে” বটকৃষ্ণ বললেন, “আমার মতন গাদা বন্দুকের নলের মুখে বসে কোন বেটা প্রেম করেছে? আমি করেছি। লরির মধ্যে বসে, কাইজারকে ডগ বিস্কুট আর আফিং খাইয়ে—রাজ্যের পোকামাকড়ের কামড় খেতে খেতে পাক্কা এক বছর। গরম গেল, বর্ষা গেল, বসন্ত গেল—প্রেমের রেলগাড়ি চলতেই লাগল, যখন তখন উল্টে যাবার ভয়। তোমার নলিনীদিদির আজ এ-রকম দেখছ ; কিন্তু তখন যদি দেখতে—কী সাহস, কত বুদ্ধি। কত রকম ফন্দিফিকির করে—ছোট বোনকে হরদম কৃমি-বিনাশক জোলাপ খাইয়ে, ছোট ভাইকে দু-এক আনা পয়সা ঘুষ দিয়ে অভিসার করতে আসত। মেয়েছেলে হয়ে টিকটিকিকে ভয় পায় না এমন দেখেছ কখনো? তোমার দিদি সে-ভয়ও পেত না। আমরা দু’জনে লরির মধ্যে বসে ফিসফাস করে কথা বলতাম, হাতে হাত ধরে বসে থাকতাম, মান করতাম, মান ভাঙাতাম। বার কয়েক ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছি। একবার তো রায়সাহেব হাতে-নাতে ধরে ফেলতেন—শুধু তাঁর চশমাটা চোখে ছিল না বলে বেঁচে গিয়েছিলাম।”
নলিনী মাথার কাপড়টা ঠিক করে নিলেন আবার, টিপ্পনী কেটে বললেন, “যা সিঁধেল চোর, সারা গায়ে তেল মেখে আসতে। তোমায় কে ধরবে।”
মমতা একটু গুছিয়ে বসলেন। তাঁর শরীর বেদম ভারী নয়। তবু বেতের চেয়ারটা শব্দ করে উঠল।
বটকৃষ্ণ চুরুটটা আবার জ্বালিয়ে নিলেন। পাশের বাংলোয় আইভিরা গ্রামোফোন বাজাতে শুরু করেছে।
বটকৃষ্ণ বললেন, “নাটকের সেকেন্ড অ্যাক্ট এইভাবে শেষ হয়ে গেল ; ভাঙা লরিতে বসে—কাইজারকে ডগ বিস্কুট আর মাঝে মাঝে আফিং-রুটি খাইয়ে। এমন সময় মাথার ওপর বজ্রাঘাত হল। নলিনী বলল, রায়সাহেব কারমাটারে যে বাড়ি তৈরি করেছেন নতুন—সেখানে হাওয়া বদলাতে যাবেন। পুরো শীতটা থাকবেন। আর সেখানেই নাকি কে আসবে নলিনীকে দেখতে। ভেবে দেখো ব্যাপারটা, একে নলিনী থাকবে না, তায় আবার কে আসবে মেয়ে দেখতে। নলিনী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে, আমি বুক চাপড়াই। আজকালকার দিন হলে অন্য কথা ছিল—ইলোপ করে নিয়ে যেতাম নলিনীকে। সেটা তো সম্ভব নয়। আর রায়সাহেব করুণাময় গুহর বাড়ি থেকে মেয়ে বার করে নিয়ে যাবার হিম্মত কার আছে। …আমরা দুটি যুবক-যুবতী তখন অকূল পাথারে ভাসছি। এক একবার মনে হত—অ্যারারুটের সঙ্গে ধুতরো ফুলের বিচি মিশিয়ে খেয়ে ফেলি। তাতে কী হত সেটা অবশ্য জানতাম না। নলিনী কেঁদে কেঁদে শুকিয়ে গেল, নলিনী মুদিল আঁখি। আর আমার তো সবদিকেই শ্মশান—খাঁ খাঁ করছে! …এমন অবস্থায় নলিনী হঠাৎ একদিন এক বুদ্ধি দিল। মেয়েরা ছাড়া কোনো বুদ্ধি কেউ দিতে পারে না। পুরাণে আছে—লক্ষ্মী বুদ্ধি দিয়েছিল বলে দৈত্যরা স্বর্গ জয় করতে পারেনি। যতরকম কুট, ফিচেল, ভীষণ ভীষণ বুদ্ধি জগৎ সংসারে মেয়েরাই দেয়।”
নলিনী আর মমতা দু’জনেই প্রবল আপত্তি তুললেন “সব দোষ মেয়েদের! তোমরা আর ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানো না?”
বটকৃষ্ণ হেসে বললেন, “মাছ ভাজা হলে আমরা খেতে জানি। কিন্তু মাছটা ভাজে কে? মেয়েরা। ও কথা থাক, তবে এটা তো সত্যি কথা—নলিনী যদি বুদ্ধিটা না দিত—আমার চোদ্দো পুরুষের সাধ্য ছিল না—অমন একটা মতলব মাথায় আসে।”
মমতা বললেন, “বুদ্ধিটা কী?”
“বলছি। রায়সাহেব করুণাময়ের হৃদয়ে অন্য কোনো করুণা না থাকলেও মানুষটির কয়েকটি বিগ বিগ গুণ ছিল। ভেরি অনেস্ট, কথার নড়চড় করতেন না—হ্যাঁ তো হ্যাঁ—না তো না। তোষামোদ খোসামোদ বরদাস্ত করতেন না একেবারে। আর ভদ্রলোকের সবচেয়ে বেশি দুর্বলতা ছিল সাধু-সন্ন্যাসীর ওপর। গেরুয়া দেখলেই কাত, হাত তুলে দু বার হরিনাম করলেই করুণাময়ের হৃদয়ে করুণার নির্ঝর নেমে আসত। নলিনী আমার হাত ধরে বলল একদিন, সোনা—তুমি সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে যাও।”
মমতা হেসে বললেন, “ও, মা সেকি কথা, দিদি আপনাকে সাধু-সন্ন্যাসী হয়ে যেতে বলল?”
নলিনী বললেন, “তুই ওসব বানানো কথা শুনিস কেন? সবই দিদি বলছে, আর উনি গোবর গণেশ হয়ে বসে আছেন, ঘটে বুদ্ধি খেলছে না!”
বটকৃষ্ণ বনেদি ঘড়ির আওয়াজের মতন বার দুই কাশলেন, তারপর বললেন, “আমার ঘটে বুদ্ধি খেলেনি—তা তো আমি বলিনি। তুমি আমায় সোনা লক্ষ্মী দুষ্ট—এইসব করে গলিয়ে শেষে বেকায়দা বুঝে গেরুয়ার লাইনে ঠেলে দিয়ে পালাতে চেয়েছিলে। তা আর আমি বুঝিনি—”
নলিনী বোনকে বললেন, “কথার ছিরি দেখছিস?
“তোমার দিদি আমায় পথে ভাসাচ্ছে দেখে—বুঝলে ভাই মমতা, আমার বুদ্ধির ঘট নড়ে উঠল। লোকে দত্তদের কি যেন একটা গালাগাল দেয়—আমি হলাম সেই দত্ত। ভেবে দেখলাম—রায়সাহেব করুণাময়কে বাগাতে হলে গেরুয়ার লাইন ছাড়া লাইন নেই। ওই রন্ধ্রপথেই ঢুকতে হবে। নলিনীকে বললাম—ঠিক আছে, তোমরা কারমাটারে যাও—আমি আসছি। নলিনী আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি এসো লক্ষ্মীটি, আমি তোমার জন্যে হাঁ করে চেয়ে থাকব।”
সত্যপ্রসন্ন এবার বেশ জোরে হেসে উঠলেন। “দাদা কি সত্যি সত্যিই সাধু-সন্ন্যাসী হলেন?”
বটকৃষ্ণ চুরুটের ছাই ঝেড়ে আবার সেটা ধরিয়ে নিলেন। বললেন, “নাটকের সেটাই তো ভাই থার্ড অ্যাক্ট। তোমার দিদিরা কারমাটারের নতুন বাড়িতে চলে গেল। রায়সাহেবের সেই নেড়ি কুকুরটা পর্যন্ত। আমার চোখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অন্ধকার হয়ে গেল। কিন্তু পুরুষমানুষ আমি—যোগী হয়ে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে কেন, শাস্ত্রে বলেছে—কর্ম আর উদ্যোগের দ্বারাই পৌরুষের বিচার। আমিও হাত পা ঝেড়ে উঠে বসলাম।”
মমতা বললেন, “কী করলেন?”
বটকৃষ্ণ বললেন, “লোকে মা বাপ মরলে মাথা নেড়া করে। আমি তোমার দিদিকে পাবার আশায়, আর করুণাময়ের করুণা উদ্রেকের জন্যে মাথা নেড়া করলাম, টকটকে গেরুয়া বসন পরলাম—আর একটা পকেট সংস্করণ গীতা আলখাল্লার পকেটে ঢুকিয়ে একদিন পৌষ মাসের সকালে কারমাটার স্টেশনে নামলুম। চোখে একটা চশমাও দিয়েছি, গোল গোল কাচ, চশমার ফ্রেমটা নিকেলের। চেহারাটা আমার ভগবানের কৃপায় মন্দ ছিল না, তা ছাড়া তখন কচি বয়েস, ড্রেসটা আমায় যা মানিয়েছিল—না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারবে না। …তা কারমাটার স্টেশনে নেমে একটু খোঁজখবর করে খানিকটা এগুতেই দেখি—আমার নলিনী মর্নিং ওয়াক করতে বেরিয়েছে। দেখে চক্ষু সার্থক হল। কে বলবে—এই নলিনী সেই নলিনী। পনেরো বিশ দিনেই দেখি ওঁর মুখ চোখের রং ফিরে গিয়েছে। সেকালে মেয়েরা আজকালকার মতন করে শাড়ি জামা জুতো পরত না। এই ফ্যাশনটাও ছিল না। নলিনী পার্শি ঢঙে শাড়ি পরেছে, গায়ে গরম লং কোট, মাথায় স্কার্ফ, পায়ে মোজা আর নাগরা জুতো। নলিনীর সঙ্গে বাড়ির ঝি নিত্যবালা। কাছাকাছি আসতেই নলিনী দাঁড়িয়ে পড়ল। একেবারে থ। তার চোখের পলক আর পড়তে চায় না। এদিকে পৌষ মাসের ওই ভোরবেলায় শীতে আমার অবস্থা কাহিল। একটা করকরে র্যাপার ছাড়া আর কোনো শীতবস্ত্র নেই। গায়ে অবশ্য তুলে ধরানো গেঞ্জি রয়েছে। কিন্তু তাতে শীত বাগ মানানো যাচ্ছে না। দিদিমণিকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে নিত্যবালা দাঁড়িয়ে পড়েছিল। নলিনী কথা বলতে পারছে না। আমিও চুপচাপ একটা কথা বলি—নলিনীদের বাড়ির কেউ আমাকে চিনত না। চোখে দেখে থাকবে—কিন্তু তেমন করে নজর করেনি। তার ওপর আমার নেড়া মাথা সন্ন্যাসীর বেশে চেনা মুশকিল। নলিনী চোখের ইশারায় আমায় মাঠ ভেঙে সোজা চলে যেতে বলল। বলে সে নিত্যকে নিয়ে স্টেশনের দিকে এগিয়ে গেল।”
মমতা ঠাট্টা করে বললেন, “দিদি আপনাকে দেখে কেঁদে ফেলেনি তো?”
“কাঁদো কাঁদো হয়ে গিয়েছিল,” বটকৃষ্ণ বললেন, “তোমার দিদি হয়তো ভাবেইনি—সেই উৎপাত আবার এসে জুটবে।”
নলিনী বললেন, “উৎপাত ছাড়া আর কি! যে জ্বালান জ্বালিয়েছে।”
সত্যপ্রসন্ন আবার সিগারেট ধরালেন, “তারপর কী হল?”
বটকৃষ্ণ বললেন, “তারপর আমি সোজা করুণাময়ের বাড়িতে গিয়ে হাজির। নতুন বাড়ি করেছেন রায়সাহেব, শৌখিন ছোট্ট বাড়ি, তখনও সব কাজ শেষ হয়নি, জানলা দরজায় সদ্য রং হয়েছে, বাড়ির বাইরে রং পড়ছে। চুনের গন্ধ, রঙের গন্ধ। তবে সত্য, জায়গাটি সত্যিই চমৎকার। রায়সাহেব বাড়ির মধ্যে কাইজারকে নিয়ে পদচারণা করছিলেন। কাঠের নতুন ফটকের সামনে আসতেই কাইজার বেটা হাউমাউ করে তেড়ে এল। কিন্তু আমার পকেটে তো তখন ডগ বিস্কুট নেই, আফিং দেওয়া বান রুটিও নেই। কাইজারের তাড়ায় গেটের সামনে থেকে পিছিয়ে এলুম। রায়সাহেবের চোখ পড়ল। তিনি একটা ঢোললা পাজামা, গায়ে জব্বর ওভারকোট পরে, গলায় মাফলার জড়িয়ে পায়চারি করছিলেন, আমায় দেখে এগিয়ে এলেন। কাইজারকে ধমক দিয়ে বললেন ; ডোন্ট শাউট। তাঁর এক ধমকেই কাইজার লেজ নাড়তে লাগল। রায়সাহেব আমায় কয়েক মুহূর্ত দেখলেন, মানে নিরীক্ষণ করলেন। আপাদমস্তক, সেই সার্চ লাইটের মতন চোখের দৃষ্টিতে আমি ভিতরে ভিতরে কাঁপতে লাগলাম। অবশ্য শীতটাও ছিল প্রচণ্ড। শেষে রায়সাহেব বললেন, কি চাই?…আমি বললুম, কিছু না। এখান দিয়ে যাচ্ছিলুম, নতুন বাড়িটা দেখে চোখ জুড়ল, তাই দেখতে এসেছিলাম। বাড়িটি বড় চমৎকার। রায়সাহেব তোষামোদে খুশি হবার লোক নন, কিন্তু বউ, বাড়ি আর গাড়ির গুণগান গাইলে পুরুষমানুষে খুশি হয়। রায়সাহেব বললেন, আচ্ছা ভেতরে আসুন। আমি হাত জোড় করে বললাম, আমায় আপনি বলবেন না, বয়স্ক প্রবীণ লোক আপনি—আমি লজ্জা পাব। ভেতরে যাবার প্রয়োজন কী! বাইরে থেকেই দেখে বড় ভাল লাগছে। রায়সাহেব আরও খুশি হলেন। বললেন, এসো, এসো ; ভেতরে এসো। তোমার তো শীত ধরে গেছে—এসো এক কাপ গরম চা খেয়ে যাও। রায়সাহেব কাঠের ফটক খুলে ধরলেন।”
মমতা হেসে গড়িয়ে পড়ে বললেন, “আপনার তো পোয়া বারো হল।”
বটকৃষ্ণ বললেন, “তা আর বলতে। রায়সাহেব তো জানেন না কোন রন্ধ্রপথে আমি ঢুকতে চাইছি। একেই বলে ভাগ্য। ভাগ্য যদি দেয় তুমি রাজা, না দিলে ফকির। অমন জাঁদরেল রায়সাহেব আমায় বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে বসালেন। চা এল। চা খেতে খেতে বললেন : তোমার বয়েস কত হে? বললাম, ছাব্বিশ শেষ হয়েছে। উনি বললেন, তা এই বয়সে সন্ন্যাস নিয়েছ কেন?
“বললাম, বয়েস কি বৈরাগ্যকে আটকায়! গৌতম বুদ্ধ কোন বয়সে গৃহত্যাগ করেছিলেন? তীর্থংকর কখন করেছিলেন? মহাপ্রভু কোন বয়সে সংসার ত্যাগ করেছিলেন তা তো আপনি জানেন। রায়সাহেব আমার মুখের দিকে দু দণ্ড তাকিয়ে থেকে বললেন, বুঝেছি। তা এখন কদিন এখানেই থাকো। পরে আমি দেখছি।”
সত্যপ্রসন্ন বললেন, “বলেন কি দাদা, সোজাসুজি আপনাকে থাকতে বললেন।”
“বললেন”, মাথা নেড়ে নেড়ে বললেন বটকৃষ্ণ। “বলেছি না—গেরুয়াতে রায়সাহেব হৃদয় গলত। তা ছাড়া উনি সন্দেহ করেছিলেন—আমি কোনো কারণে বাড়ি থেকে পালিয়ে সাধু-সন্ন্যাসী সেজেছি।”
নলিনী বোনকে বললেন, “জানিস মনো, আমাদের কারমাটারে বাড়ির দশ আনা হয়েছে মাত্র—ছ’ আনা তখনও বাকি। দোতলায় মাত্র দুটো ঘর হয়েছে, একটায় থাকত বাবা ; আর অন্যটায় মা, যামিনী, কালু। নীচের তলায় একটা মাঝারি ঘরে থাকতুম আমি। নীচেই ছিল রান্না, ভাঁড়ার, বসার ঘর।—তবু কোথাও কোথাও কাজ বাকি থেকে গেছে। বাবা ওকে নীচের তলার বসার ঘরটায় থাকতে দিল।”
বটকৃষ্ণ বললেন, “তোমার বাবার মতন সদাশয় মানুষ আর হয় না। থাকতে দিলেন বটে কিন্তু চারদিক থেকে গার্ড করে দিলেন। সকালে রায়সাহেব নিজে এসে আমার ধর্মে কতটা মতি তা বাজিয়ে দেখার চেষ্টা করতেন। ভীষণ ভীষণ প্রশ্ন করতেন : রামায়ণ মহাভারত থেকে গীতা পর্যন্ত। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জানার চেষ্টা করতেন আমি কে—কোথা থেকে এসেছি—কেন সংসার ত্যাগ করেছি? সকালে আমাকে ধরাশায়ী করে তিনি বেরিয়ে যেতেন। তিনি বেরিয়ে গেলে আসত ভবিষ্যৎ শ্যালিকা যামিনী আর শ্যালক কালু। ওরা এসে বলত, লুডো খেলো ; কিংবা বলত-মাথা নিচু পা উঁচু করে তপস্যা করে দেখাও, না হয় দুটো বেয়াড়া অঙ্ক এনে বলত, করে দাও। দুপুরবেলা আমার শাশুড়ি পেঁপে সেদ্ধ কাঁচকলা সেদ্ধ ডাল সেদ্ধ দিয়ে ভাত খাওয়াতেন। রায়সাহেব কারমাটারের সস্তা মুরগির ঝোল টানতেন। পঙিক্ষ চাকর, নিত্য ঝি এরাও আমাকে চোখে চোখে রাখত। সন্ধেবেলায় রায়সাহেব আবার একদফা গোয়েন্দাগিরি করতে বসতেন। রাত্রে কাইজারকে ছেড়ে রাখা হত নীচের তলায়। ভেবে দেখো, অবস্থাটা কী দাঁড়াল। একেবারে প্রিজনার হয়ে গেলাম। ভাবতাম হায়—একি হল, আমি তো নজরবন্দি হয়ে গেলাম। এরপর রায়সাহেব আমার মতলবটা জানতে পারলেই তো সোজা পুলিশের হাতে তুলে দেবেন।”
মমতা রঙ্গ করে বললেন, “দিদির সঙ্গে দেখা হত না?”
“দিদির এদিকে ঘেঁষার হুকুম ছিল না। দৈবাৎ দেখা হয়ে যেত।”
নলিনী এবার গালে হাত বললেন, “কত মিথ্যেই যে বলবে! আমি তোমায় দুবেলা চা জলখাবার দিতে আসতুম, ঘর পরিষ্কার করতে যেতাম।”
“ও তো নিমেষের ব্যাপার। আসতে আর যেতে। বড় জোর একটা চিরকুটে দু লাইন লিখে ফেলে দিয়ে যেতে। তোমার ন্যাকামি দেখলে তখন রাগে গা জ্বলে যেত। নিজেরা চারবেলা চর্বচোষ্য খাচ্ছ, ডিম উড়ছে, মুরগি উড়ছে, মাছ চলছে—রাত্রে নাক ডাকিয়ে নিদ্রা হচ্ছে—আর আমি বেটা বটকৃষ্ণ—ভেজানো ছোলা, আদার কুচি, কাঁচকলা সেদ্ধ, কপি সেদ্ধ খেয়ে বেঁচে আছি। রাত্রে মশার ঝাঁক গায়ের চামড়া ফুলিয়ে দিচ্ছে, তার ওপর ওই নেড়ি কুকুরটার সারা রাত দাপাদাপি।”
নলিনী বললেন, “দেখো দত্তবাবু, এত পাপ ভগবানে সইবেন না। তোমার জন্যে আমি লুকিয়ে ডিমের ওমলেট, মাছ ভাজা, এমন কি কাচের বাটি করে জানলা গলিয়ে মাংস পর্যন্ত রেখে গিয়েছি। মশার জন্যে রোজ ধুনো দিয়ে যেতাম তোমার ঘরে।”
বটকৃষ্ণ বললেন, “ধুনো যে কোথায় দিতে লক্ষ্মী তা তো জানি না। তবে হ্যাঁ, তোমার বাবা কাইজারকে রোজ হাড় মাংস খাইয়ে খাইয়ে একটা বাঘ করে ফেলেছিলেন। আফিং খাইয়ে খাইয়ে আমি নেড়িটার শরীর চিমসে করে দিয়েছিলাম। তোমার বাবা তাকে আবার তাজা করে ফেলেছিলেন। রাত্রে একটু বেরুব, রোমিও-জুলিয়েট করব—তার কি উপায় রেখেছিলেন রায়সাহেব! চার পাঁচ দিনেই বুঝলুম, আমার আশা নেই। বৃথাই মাথা নেড়া করে গেরুয়া পরে ছুটতে ছুটতে এসেছি। নলিনী-মিলন হবে না। মানে মানে ফিরে যেতে পারলেই বাঁচি। তবে হ্যাঁ—সংসারে আর ফিরব না। গেরুয়াই যখন ধরেছি—তখন সোজা হরিদ্বার কিংবা কনখলে চলে যাব। এটা স্থির করে নিয়ে রায়সাহেবকে বললাম, এবার আমায় যেতে দিন। উনি বললেন, সেকি আরও কটা দিন থাকো না। অসুবিধে হচ্ছে! বললাম, আজ্ঞে না, এত সুখ-আরাম আমাদের জন্যে নয়। আমরা গৃহত্যাগী। দুঃখকষ্ট সহ্য করাই আমাদের ধর্ম। রায়সাহেব ধূর্ত চোখ করে বললেন, ছেলেমানুষ তো, ফাজলামি বেশ শিখেছ। শোন হে, এই রবিবার মধুপুর থেকে আমার এক বন্ধু আসবে। রিটায়ার্ড পুলিশ অফিসার! আমারও ঘরদোর কম। তা তুমি কালকের দিনটা থেকে পরশু—শনিবার চলে যেও।
মমতা বললেন, “ওমা! সেকি! আপনাকে চলে যেতে বললেন?”
“বললেন বই কি। সাফসুফ বললেন—” বটকৃষ্ণ মাথা নাড়লেন! “আমিও ভেবেছিলুম—চলেই যাব। জেলখানায় বসে কিছু তো করার উপায় নেই। সেদিন সন্ধেবেলায় তোমার দিদি যখন কাঠকয়লা জ্বালিয়ে ধুনো দিতে এল, বললাম—তোমার বাবা আমায় পরশুদিন চলে যেতে বলেছেন। আমি চলে যাচ্ছি। তোমাদের ঘরদোর কম ; মধুপুর থেকে তোমার বাবার কোন বন্ধু আসবেন। তোমার দিদি ধুনোয় ঘর অন্ধকার করে দিয়ে চলে গেল। আমি বসে নাকের জলে চোখের জলে হলাম। রাত্রের দিকে তোমার দিদি এক চিরকুট ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল। চিরকুট পড়ে আমার মাথা ঘুরতে লাগল। মধুপুরের সেই ভদ্রলোক—রায়সাহেবের বন্ধু—তাঁর ভাইপোর জন্যে নলিনীকে দেখতে আসছেন। তোমার দিদি লিখেছিল : তুমি আমায় বাঁচাও। না বাঁচালে বিষ খাব। তুমি ছাড়া আমার কে আছে লক্ষ্মীটি?”
সত্যপ্রসন্ন নলিনীর দিকে চেয়ে বললেন, “আপনি কি তাই লিখেছিলেন, দিদি?”
নলিনী বললেন, “বয়ে গেছে।”
বটকৃষ্ণ বললন, “বয়েই তো যাচ্ছিল। অন্য হাতে পড়লে বুঝতে। সোনার অঙ্গ কালি করে দিত।…যা বলছিলাম সত্য, তোমার দিদির চিঠি পড়ে আমার মনে হল—বিষটা আমিই আগে খেয়েনি। কিন্তু কোথায় পাব বিষ? কারমাটারে একটা সিদ্ধির দোকান পর্যন্ত নেই। ভাবলাম গলায় দড়ি দি; ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখি—একটা হুক পর্যন্ত নেই, দড়ি বাঁধব কোথায়! যেদিকে তাকাই ফাঁকা। মরার মতন কিছু হাতের কাছে পেলাম না। ভাবি আর ভাবি, কোনো উপায়ই পাই না। হঠাৎ একটা জেদ চাপল। ভাবলাম, জীবনটা তো নষ্ট হয়েই গেল, প্রেমের পূজায় এই তো লভিনু ফল। তা নষ্টই যখন হল—বেচারি নলিনীর জন্যে কিছু না করেই কি মরব? ও আমার কাছে বাঁচতে চেয়েছে। কেমন করে বাঁচাই? কেমন করে? সারা রাত ঘুম হল না। ছটফট ছটফট করে কাটল। হাজার ভেবেও কোনো বুদ্ধি এল না। পরের দিন সকাল থেকে মৌনী হয়ে থাকলাম। রায়সাহেবকেও পাত্তা দিলাম না। দুপুরবেলায় খেলাম না। বিকেলবেলায় কেমন ঘোরের মতন বাইরে পায়চারি করতে করতে খেয়ালই করিনি রায়সাহেব আমায় ডাকছেন। যখন খেয়াল হল—রায়সায়েব তখন আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। উনি বললেন, কি হে, তুমি কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁট নাকি? বলতে যাচ্ছিলাম—আজ্ঞে না। কিন্তু হঠাৎ আমার এক মামার কথা মনে পড়ল। মামা সোমনামবুলিজমে ভোগে, মানে স্লিপ ওয়াকার, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হাঁটে, তবলা বাজায়, ক্যালকুলাসের অঙ্ক করে। বললাম, আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার ওই রোগটা আছে। বংশানুক্রমিক। রায়সাহেব আঁতকে উঠে বললেন, সেকি, আগে তো বলোনি। ও যে সর্বনেশে রোগ। আমার এক বন্ধু এই রোগে সেলুন থেকে লাফিয়ে পড়ে মারা গেল। এ তো ভাল কথা নয়। তুমি রাত্রে বাথরুম-টাথরুমে বেরিও না। কাইজার ছাড়া থাকে। তোমার গলার টুঁটি কামড়ে ধরবে। না না, খুব খারাপ, ভেরি ডেনজারাস, তোমার আগেই বাপু বলা উচিত ছিল। স্লিপ ওয়াকার্সদের আমি বড় ভয় পাই। রায়সাহেব কি যেন ভাবতে ভাবতে চলে গেলেন। আমিও হঠাৎ ব্রেন ওয়েভ পেয়ে ভাবতে ভাবতে ঘরে ফিরে গেলাম।”
মমতা শুধোলেন, “মাথায় বুঝি কোনো বুদ্ধি এল?”
বটকৃষ্ণ চুরুটটা ধরিয়ে নিলেন আবার। বললেন, “হ্যাঁ, মাথায় বুদ্ধি এল। ওই একটি মাত্র পথ ছাড়া আর কোনো পথও ছিল না। রাত্রে এক ফাঁকে তোমার দিদিকে অনেক কষ্টে ধরলাম। বললাম, সোনা আমার—তোমার শোবার ঘরের দরজাটা আজ একটু খুলে রেখো। শুনে তোমার দিদি আমায় মারতে ওঠে আর কি! অনেক করে বোঝালাম। বললাম—তোমার বাবা কত বড় বাঘা ওল আমি দেখব, আমিও সেই রকম তেঁতুল।”
অধৈর্য হয়ে মমতা বললেন, “তারপর কি করলেন বলুন।”
বটকৃষ্ণ বললেন, “সেদিন রাত্রে রায়সাহেব কাইজারকে দোতলায় নিয়ে গিয়ে বেঁধে রাখলেন। তোমার দিদি শুতে নীচে, তার ঘরে থাকত নিত্য ঝি। নিত্য বড় ঘুম কাতুরে। ভূতটুতের বড় ভয়। সেদিন নিত্য ঘুমিয়ে পড়ার পর নলিনী ঘরের ভেতর থেকে ছিটকিনিটা খুলে রাখল। ভোর রাতের দিকে আমি স্লিপ ওয়াকিং করতে করতে তোমার দিদির ঘরে গিয়ে হাজির। নিত্যঝি ভোরবেলায় উঠত। ঘুম থেকে উঠে চোখ কচলাতে কচলাতে বিছানার দিকে তাকাতেই দেখল আমি সটান বিছানায় শুয়ে আছি, নলিনী জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে। নিত্য হাঁউমাউ করে চেঁচাতে লাগল। তার চেঁচানির চোটে কাইজার চেন ছিঁড়ে বাঘের মতন নীচে নেমে এল। পাজামার দড়ি আঁটতে আঁটতে রায়সাহেব নীচে নেমে এলেন, আমার হবু শাশুড়ি ঠাকরুণও। পঙিক্ষ চাকরও হাজির। আমি সমস্তই বুঝতে পারছি—কিন্তু নড়ছি না—মড়ার মতন শুয়ে আছি। কানে এল, রায়সাহেব ঘরের মধ্যে বোমা ফাটানোর গলায় বললেন, ঘরের দরজা কে খুলেছিল? কে? নলিনী কাঁপতে কাঁপতে কাঁদতে কাঁদতে বলল, নিত্যদি। কলঘরে গিয়ে ফিরে এসে নিশ্চয় দরজা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল। নিত্য বলল, না বাবাঠাকুর আমি নই। শাশুড়ি ধমক দিয়ে বললেন, চুপ কর তুই, তোর ঘুম আমি জানি না। সব ক’টাকে বাড়ি থেকে তাড়াব। রায়সাহেব বললেন, ওই রাস্কেল, ইতর, ছুঁচোটাকে তুলে দাও, দিয়ে আমার ঘরে নিয়ে এসো। হারামজাদাকে হান্টার পেটা করব।”
সত্যপ্রসন্ন প্যাকেট খুলে দেখলেন আর সিগারেট নেই। মমতা হাসির দমক তুলে দিদির হাত টিপে ধরলেন।
বটকৃষ্ণ বললেন, “খানিকটা পরে আমি রায়সাহেবের ঘরে গিয়ে দাঁড়ালুম। ঘরে আমার হবু শাশুড়ি ছাড়া আর কেউ ছিল না। রায়সাহেব সার্কাসের রিং মাস্টারের মতন বসে ছিলেন হান্টার হাতে, একপাশে গিন্নি, অন্য দিকে তাঁর কাইজার। রায়সাহেব আমায় দেখেই তোপ দাগলেন : বদমাশ, স্কাউড্রেল, পাজি, ইতর, কোথাকার।…তুমি কোন মতলবে বাড়ির মেয়েদের ঘরে ঢুকেছিলে? সত্যি কথা বলো? নয়ত চাবকে পিঠের ছাল তুলে দেব!…ভয়ে আমার বুক কাঁপছিল, কিন্তু এই শেষ সময়ে ভয় করলে তো চলবে না। মা কালীকে মনে মনে ডেকে ন্যাকার মতন বললুম, আপনি কি বলছেন—আমি বুঝতে পারছি না। আমি সাত্ত্বিক সন্ন্যাসী মানুষ। আমি কেন বাড়ির মেয়েদের ঘরে ঢুকতে যাব, ছি ছি। বলে কানে আঙুল দিলাম।
রায়সাহেব হান্টারটা সোঁ করে ঘুরিয়ে মেঝের ওপর আছড়ে মারলেন। তুমি সাত্ত্বিক—তুমি সন্ন্যাসী! তুমি জোচ্চোর, ধাপ্পাবাজ, লম্পট—। আমি তোমায় পুলিসে দেব।
আমি হাত জোড় করে বললুম, আপনি বৃথা উত্তেজিত হচ্ছেন।
তোমায় আমার খুন করতে ইচ্ছা করছে।
আমি কিন্তু নির্দোষ। আমার কোনো অপরাধ নেই।
তুমি নলিনীর ঘরে কেমন করে গেলে?
আজ্ঞে আমি জানি না।
জানো না? বদমাশ?
সত্যিই জানি না। বোধ হয় ঘুমের ঘোরে চলে গিয়েছি। আপনি তো জানেন আমার স্লিপ ওয়াকিং রোগ আছে। ঘুমের ঘোরে কি করি জানি না।
রায়সাহেব হান্টার তুলে আছড়াতে গিয়েও থেমে গেলেন। রায়গিন্নি বললেন, ঝি-চাকর—সবাই তো দেখল জানল। তোমার কি রোগ আছে বাছা আমি জানি না। কিন্তু এ-কথা যদি বাইরে রটে তবে যে কেলেঙ্কারি হবে। লজ্জায় আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। কাল মধুপুর থেকে তার বন্ধুর আসার কথা।
রায়সাহেব কী ভেবে আমায় আদেশ দিলেন, এখন নীচে যাও। পরে আমি যা করার করব।
আমি নীচে নেমে আসার সময় দেখি নলিনী পাশের ঘরে কাঁদছে।
ঘণ্টাখানেক পরে রায়সাহেবের কাছ থেকে স্লিপ এল। পঙিক্ষ নিয়ে এসে দিল আমায়। রায়সাহেব নিজে আর রাগে লজ্জায় ক্ষোভে নীচে আসেননি। স্লিপে ছিল, তুমি আমার মানমর্যাদা সম্মান ডুবিয়েছ। নলিনীকে তোমায় বিয়ে করতে হবে। সন্ন্যাসীগিরি চলবে না। বিয়ে না করলে পুলিশে দেব।”
বটকৃষ্ণ তাঁর গল্প শেষ করে হা হা করে হাসতে লাগলেন। বললেন “শ্বশুরমশাই পরে অবশ্য বুঝেছিলেন—তিনি একটি রত্ন পেয়েছেন। আমিও অবশ্য বড় রত্ন পেয়েছি, ভাই,” বলে বটকৃষ্ণ চোখের ইশারায় নলিনীকে দেখালেন।