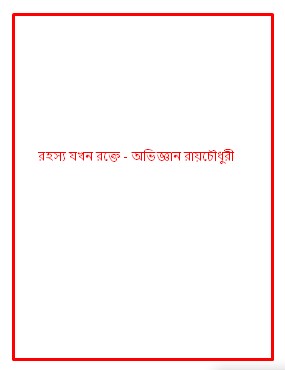- বইয়ের নামঃ রহস্য যখন রক্তে
- লেখকের নামঃ অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী
- বিভাগসমূহঃ গল্পের বই
১. এই যে পাঁচ
রহস্য যখন রক্তে – অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী
০১.
এই–এই যে পাঁচ। আর এই দ্যাখো, শেষ সাপটা টপকালাম। এবার দুই পড়লেই উঠে যাব।
–দেখো, তবু আমিই জিতব। আমি আগে ওখানে পৌঁছে যাব।
–আচ্ছা সোনা, ঠিক আছে, তুমি-ই জিতবে। তুমি সবসময় জিতবে। পিকুর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় জয়ন্ত।–এবার তোমার দান।
পিকু মিনিট খানেক ধরে বেশ নেড়েচেড়ে দান ফেলে। ছক্কাটা টালমাটাল করে দুই এ এসে দাঁড়ায়।
যাঃ, এক্কেবারে সাপের মুখে সাপটা আবার খেয়ে নিল।
না–আমি আর খেলব না। ছক্কাটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে উঠে পড়ে পিকু। ছুটে শোওয়ার ঘরে গিয়ে ঢোকে। খাটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর জোরে কেঁদে ওঠে। পিকু যখন কাঁদে তখন কান পাতা দায়। এত জোরে কাঁদে যে আগে আশপাশের বাড়ি থেকে সবাই খোঁজ নেয় কী হল?
জয়ন্ত তাড়াতাড়ি খেলা ছেড়ে পিছু নেয়। ঘরে ঢুকে খাটের ওপর পিকুর পাশে শুয়ে পড়ে, ভোলানোর চেষ্টা করে।
–সোনা, এত তাড়াতাড়ি হাল ছাড়তে নেই। হয়তো ওই সাপটা পেরিয়ে তুই আমার আগেই উঠে যেতিস! আমার তো দুই পড়েই না!
পাঁচ বছরের ছেলেকে জড়িয়ে ধরে জয়ন্ত আদর করতে থাকে। কিন্তু অত সহজে পিকু ভোলার নয়। আশা করেছিল অন্তত এবার জিতবে। আর বাবাটাও দুষ্টু। কেমন করে অত বড় সাপগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে পেরিয়ে গেল! পিকুর লাকটাই খারাপ। বারবার ওই পঞ্চাশের আর বিরাশির বিচ্ছিরি সাপগুলো গিলে খায়। এর পরেরবার ও তবেই সাপলুডো খেলবে যদি তাতে ওই বিচ্ছিরি সাপগুলো না থাকে।
–সোনা, সব খেলাতেই হারজিত হয়। তাতে এত কাঁদে না। পরেরবার হয়তো তুমি জিতবে। জয়ন্ত বলতে থাকে–তুমি আইনস্টাইনের কথা শুনেছ?
দূর থেকে বিতানের গলা আসে,–আচ্ছা ও আইনস্টাইনের কথা কী করে জানবে? কাকে যে কী বলো!
–বাহ্, আইনস্টাইনের কথা জানবে না?
–ঠিক আছে বাবা, তুমি আইনস্টাইনের কথা বলো। পিকু বাবার পক্ষ নেয়।
–উনি ছিলেন খুব বড় বিজ্ঞানী। এই যে তুমি রিমোট দিয়ে টিভি চালাচ্ছ, ফ্যান ঘুরছে, মা মাইক্রোওয়েভে রান্না করছে, তুমি ছোট ছোট খেলনার গাড়ি নিয়ে খেলছ, আমি কম্পিউটারে কাজ করছি–সবই কিন্তু বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার। আর আইনস্টাইন ছিলেন একজন খুব বড় বিজ্ঞানী।
–বাবাই, আমাদের যে গাড়িটা আছে সেটাও কি আইনস্টাইনের বানানো?
হেসে ওঠে জয়ন্ত,না তা নয়, বিজ্ঞানীরা যে সবসময় নিজে বানান তা নয়, কীভাবে করা যায় তা বলেন। আর সবাই তো সবকিছু আবিষ্কার করেন না।
–আচ্ছা তোমার চশমাটাও কি বিজ্ঞানীদের তৈরি?
–হ্যাঁ।
–আচ্ছা বাবাই, আমাদেরও কি বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন?
না, তা নয়। বলে খানিকক্ষণ থেমে থাকে জয়ন্ত। হয়তো পরে তাও হবে। বিজ্ঞানীরাই তৈরি করবে।
–বাবাই, ঠাকুররা তাহলে কী করেন? ঠাম্মা যে বলে সব ঠাকুররা করেন।
জয়ন্ত খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর বলে,–আমরা ঠিক করছি না ভুল করছি তা ঠাকুররা বলে দেন। জানো তো, আইনস্টাইন মারা যাওয়ার সময় বলেছিলেন, আমি জীবনে একটাই ভুল করেছি আর সেটা হল অ্যাটম বোম নিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টকে। একটা চিঠি লেখা। ওই একটা চিঠির জন্যই বিশাল একটা অ্যাটম বোমা তৈরি হয়। জাপান এর দুটো আস্ত শহর তার জন্য ধ্বংস হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায়।
–বাবাই, ওই বোমাটা কি আইনস্টাইন তৈরি করেছিলেন?
না রে, আইনস্টাইন খুব ভালো লোক ছিলেন। উনি কখনও ভাবেননি যে ওনার আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে ওরকম একটা মারাত্মক বোমা তৈরি করা হবে।
জানো তো, আমারও এরকম একটা সমস্যা হয়েছে।
কীরকম? তোর আবার কী সমস্যা?
–দীপুকে চেনো? ও খুব দুষ্টু। আমি মাটি আর ইটের টুকরো দিয়ে একটা বল তৈরি করেছিলাম। ও সেটাকে ছুঁড়ে রুজুদের কাচের জানলা ভেঙে দিয়েছে কাল।
–সে কী? মাকে বলেছিস?
–নাহ, আমরা পালিয়ে এসেছি। ওরা দেখতে পায়নি। আর রুজু আমাকে কাল খেলতেও নেয়নি। ভালোই হয়েছে।
বিতান, ও বিতান, শুনেছ? জয়ন্ত ঘর ছেড়ে রান্নাঘরের দিকে যায়, কাল পিকুরা রুজুদের কাচের জানলা নাকি বল দিয়ে ভেঙে দিয়েছে!
.
০২.
হ্যালো–বিতান বলছি–হ্যালো…
রিং হতে বিতান এসে ফোন ধরেছিল। উলটোদিকের কথা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে না। কীরকম একটা ঘ্যাসঘেসে আওয়াজ।
আরো খানিকক্ষণ উত্তর না পেয়ে বিতান ফোনটা রেখে আবার রান্নাঘরে এসে ঢোকে। জয়ন্ত অফিসের কাজে বাইরে গেছে। আসবে আরও দশদিন পরে। এ কদিন রান্নার বিশেষ ঝামেলা নেই। তবু একটা কিছু তো তৈরি করতে হবে। আজও রান্নার লোক আসেনি।
ফোনটা আবার বাজছে।
–দেখতো সোনা, কার ফোন। রান্নাঘর থেকে চেঁচিয়ে বলে ওঠে বিতান।
টিভিতে টম অ্যান্ড জেরি ছেড়ে ছুটে এসে ফোন ধরে পিকু। হ্যালো, আমি পিকু বলছি।
ওদিক থেকে কারও কথা শুনতে পায় না।
কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে পিকু। বলে,–মা, কেউ কিছু বলছে না।
–অ্যাই, কে না জেনে ফোনে ওরকমভাবে কথা বলে না। দাঁড়া, আমি ধরছি।
বেরিয়ে এসে বিতান ফোনটা ধরে, হ্যালো, কে? শোনা যাচ্ছে না। কান্ট হিয়ার ইউ।
ফোনের উলটোদিকে তবু নীরবতা। পুরো নীরবতা নয়, পিছন থেকে অস্পষ্ট একটা আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। যেন অনেক দূরে কেউ ফোনে কথা বলছে।
হ্যালো? বিরক্ত হয়ে আরও মিনিট দুয়েক ধরে থেকে ফোন ছেড়ে দেয় বিতান। ছেড়েই মনে হয় ফোনটা জয়ন্তর নয় তো?
জয়ন্ত আমেরিকায় পৌঁছে একটা নতুন ফোন নাম্বার দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই নাম্বারে ফোন করে বিতান। ফোনটা সুইচড অফ। অস্বাভাবিক কিছু নয়। অনেক সময়েই জয়ন্ত সেলফোন চার্জ করতে ভুলে যায়। আর তা ছাড়া এখন ভারতে বিকেল চারটে, অর্থাৎ নিউইয়র্কে সকাল সাড়ে ছটা। এসময় হয়তো ফোনটা ইচ্ছে করেই অফ করে রেখেছে, যাতে কেউ বিরক্ত না করে, আচ্ছা, আজকেই তো ওর নিউইয়র্ক থেকে ডেট্রয়েট যাওয়ার কথা। মর্নিং ফ্লাইটে। ও তাহলে এখন ফ্লাইটেই আছে। আর তাই ফোন সুইচড অফ।
আজকে পিকুর ছুটি ছিল। অত্যধিক গরম পড়ায় স্কুলে ছুটি দিয়েছে। এবারে কলকাতায় গরমটা খুব বেশি মাত্রায় পড়েছে। পিকু একটা ছবি আঁকতে বসেছে।
–মা, বাবাই কবে আসবে?
–আচ্ছা, তুই রোজ একই প্রশ্ন করিস কেন বলতো? কালকেই তো বললাম, দশদিন
–তার মানে আজকের পরে ঠিক নদিন?
–হ্যাঁ, তুই একটা কাজ কর। ক্যালেন্ডারে লিখে রাখ। বাবাইকেও তো রোজ এক প্রশ্ন করিস।
জানো তো বাবাই সেদিন বলল যে বাবাই নাকি সায়েন্টিস্ট। সত্যি বাবাই সায়েন্টিস্ট? আইনস্টাইনের মতো?
হেসে উঠল বিতান,বাবাই হল ইঞ্জিনিয়ারসফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। সায়েন্টিস্ট ঠিক নয়। তোর সঙ্গে মজা করেছে। তা আজ সকালে অত কী কথা হচ্ছিল বাবাই-এর সঙ্গে ফোনে? রাতেও বাবাইকে ঘুমোতে দিসনি!
বাবাই আমাকে অনেক গল্প বলছিল। বলছিল একটা যুদ্ধের কথা। অৰ্জুন বলে একটা রাজা যুদ্ধ করতে চাইছিল না। তা কৃষ্ণ ঠাকুর নাকি ওকে বলেছিল যে সবই তো আগে থেকে ঠিক করা আছে। ও যুদ্ধ করুক না করুক তাতে কিছু আসে যায় না।…মা, এটা কি সত্যি?
–হ্যাঁ, মহাভারতের কথা। আমি একদিন গল্পটা পড়ে শোনাব।
–না, তুমি গল্প বলতেই পারো না। তুমি বললে দু-মিনিটেই গল্প শেষ হয়ে যায়। বাবাই কী সুন্দর গল্প বলে। আমি বাবাই-এর কাছে শুনব।
জয়ন্তর সত্যি ধৈর্য আছে। আর ছেলেকে এত ভালোবাসে আর সময় দেয়! যত ব্যস্তই থাকুক, ঠিক সময় বার করে ওর সঙ্গে খেলবে, ওর সঙ্গে গল্প করবে। এই তো আমেরিকায় গিয়েও রোজ ছেলের সঙ্গে ফোনে গল্প করে। কোনওদিনও বাদ যায় না।
বাইরে কলিংবেল বেজে উঠল। ঘর পরিষ্কারের মেয়েটা এসেছে নিশ্চয়ই। দরজা খুলতে যাবে, আবার ফোনে রিং। দরজা খোলে বিতান। কাজের মেয়ে মিনতি এসেছে। ফোনে রিং হয়েই চলেছে। ফোনটা দৌড়ে এসে ধরে বিতান।
উলটো দিকের কণ্ঠস্বর পরিষ্কার আমেরিকান অ্যাকসেন্টে ইংরেজিতে বলে ওঠে,–আপনি কি জয়ন্তর স্ত্রী?
–হ্যাঁ বলুন।
–আমি জয়ন্তর অফিস থেকে বলছি। ওর আমেরিকার অফিসের কোলিগ আমি। আমার নাম মাইক।
কি–কিছু অসুবিধে হয়েছে জয়ন্তর?
কণ্ঠস্বর খানিকক্ষণ থেমে থাকে। দ্বিধাজড়ানো গলায় বলে ওঠে,দশমিনিট আগে আমরা খবর পেয়েছি জয়ন্ত যে ফ্লাইটে ডেট্রয়েট যাচ্ছিল সেটা ক্র্যাশ করেছে। ফ্লাইটে কেউ বেঁচে আছে। কিনা আমরা সে খবর এখনও পাইনি।
খানিক থেমে মাইক ফের বলে,–দুঃখ জানানোর কোনও ভাষাই নেই আমার কাছে। এত মর্মান্তিক ঘটনা। আমরা এখান থেকে সবরকম সাহায্যের ব্যবস্থা করছি।
মাইক থেমে যায়। অন্যপ্রান্তে যে বিতান আর নেই তা টের পেয়েছে।
ফোনটা হাতে নিয়ে বিতান মাটিতে বসে পড়েছে। জয়ন্ত নেই! খানিক দূরে পিকু চেঁচিয়ে ওঠে, মা, বাবাই-এর ফোন? কবে আসছে?
.
০৩.
–ম্যাডাম, আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমরা রজতের সম্বন্ধে এত কমপ্লেন পাচ্ছি যে ওকে আর এই স্কুলে রাখা সম্ভব হচ্ছে না। হি ইজ নট নর্মাল। হি নিক্স ট্রিটমেন্ট।
–আপনি তো জানেনই, ওর বাবা একবছর আগে মারা যায়। এয়ার ক্র্যাশে। তারপর থেকেই ও মাঝেমধ্যে এরকম বিহেভ করে। কিন্তু আমি চেষ্টা করছি। কথা দিচ্ছি–
আচ্ছা, আপনিই বলুন আমরা অন্যান্য পেরেন্টসদের কী বলব। এই নিয়ে তিনবার হল। হঠাৎ করে ও প্রচণ্ড ভায়োলেন্ট হয়ে যাচ্ছে। তখন হাতের কাছে যা পায় তাই ছোঁড়ে। ও এখনও বিশ্বাস করে যে ওর বাবা জীবিত। কেউ সেটা মানতে না চাইলে, ও তার সঙ্গে মারপিট শুরু করে দেয়।
আমি ওকে বোঝাব। প্লিজ ম্যাম, আমাকে আর একবার চান্স দিন।
–আর অ্যাটেন্ড্যাস! অর্ধেকের বেশিদিন ও স্কুলে আসেনি। হাউ ডু ইউ এক্সপ্লেন দ্যাট?
–ও খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে মাঝেমধ্যে। আমি কথা দিচ্ছি ও আসবে–রেগুলার ক্লাস করবে এখন থেকে।
অসহায় দৃষ্টিতে বিতান প্রিন্সিপ্যালের দিকে তাকিয়ে থাকে। কী করে বোঝাবে যে স্কুল থেকেও যদি ওকে বার করে দেওয়া হয়, তাহলে কোনওভাবেই পিকুকে আর স্বাভাবিক করে তোলা যাবে না। সব ডাক্তারের একই পরামর্শ পিকুকে যতটা সম্ভব ব্যস্ত রাখতে হবে। তবেই আস্তে আস্তে ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবে। শেষে কোনওমতে প্রিন্সিপ্যাল রাজি হন। আর জানিয়ে দেন যে এবারই লাস্ট চান্স।
পিকু আজকাল আগের মতো গল্পের বই পড়ে না, খেলাধুলো করে না। কারুর সঙ্গে মেশে না। এমনকী বাবার পড়ার ঘরে পর্যন্ত ঢোকে না। মাঝেমধ্যে হঠাৎ করে খেপে ওঠে। তখন ওকে ধরে রাখাই দায় হয়। হাতের কাছে যা পায় ছুঁড়ে ফেলে। চিৎকার করে বলতে থাকে–তোমরা সবাই বিচ্ছিরি, মিথ্যেবাদী। কেউ খেলতে জানো না। গল্প বলতে জানোনা।
বিতান জানে না ওর ছেলে আর কোনওদিন স্বাভাবিক হবে কিনা। যাকে একসময় সারাক্ষণ ঘরে ছোটাছুটি করতে দেখত, সবসময় হাসিখুশি, প্রাণোচ্ছল দেখত,–সেই এখন চুপচাপ অন্ধকার। ঘরে বসে থাকে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মাঝে মাঝে মনে হয় যে একদম অন্য কোনও জগতে হারিয়ে গেছে।
এরমধ্যে দুদিন বাড়ি থেকে একা বেরিয়ে গেছে। বিপদ হতে পারত। নেহাতই বিতান খুব সতর্ক ছিল, তাই দুবারই কয়েকমিনিটের মধ্যে টের পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে লোকজন লাগিয়ে খোঁজাখুঁজি করে পেয়েছে। বাড়িতে এখন সবসময় তটস্থ হয়ে থাকে, কখন কী বিপদ হয়!
.
০৪.
কাকু, আমার কোনও চিঠি আছে? আমেরিকার থেকে?
মনোহরবাবু সাইকেল থেকে নেমে ছেলেটার দিকে তাকালেন। সেই ছেলেটাই। রোজ একই প্রশ্ন করে। দোতলা বাড়ির একতলার গ্রিল দেওয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে।
অন্যদিন কোনওরকমে না বলে চলে যান। এমনিতেই আজকাল চিঠিপত্র আদানপ্রদান। খুব কমে গেছে। দু-একটা আসে বিদেশ থেকে। তা সেটা আগে থেকেই খেয়াল থাকে। তা আজ শুধু না বলে থেমে থাকলেন না মনোহরবাবু। ছেলেটার দিকে এগিয়ে গেলেন। রোগা– বছর আটেক বয়েস হবে। চোখ দুটো খুব উজ্জ্বল–গভীর দৃষ্টি। রং রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেলেও ফরসার দিকে।
–কেন তোমার কি কারো চিঠি আসার কথা আছে?
চুপ করে থাকল ছেলেটা।
কী নাম তোমার?
–পিকু। আমার জন্য কোন আমেরিকার চিঠি নেই না?
–না বাবু। কার চিঠি?
না–এমনিই–বলে ছেলেটা ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল।
মনোহরবাবুর অজ একটু সময় আছে। দোনামনা করে বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। কলিংবেলটা টিপলেন। দু-তিনবার টেপার পরে দরজা খুলল এক মাঝবয়েসি মহিলা। মাঝারি গড়ন-সুন্দরী। মুখের দিকে তাকালে মনে হয় সারা পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ এসে দানা বেধেছে।
একটু ইতস্তত করে বলেই ফেললেন মনোহরবাবু। আমি এখানকার নতুন পিওন। মাসদুয়েক এসেছি। বারান্দায় একটা ছেলে দাঁড়িয়ে ছিলনাম বলল পিকু-ওকি আপনার ছেলে?
অন্যমনস্ক ভাবটা কেটে গেল মহিলার। মুহূর্তে সজাগ হয়ে বলে উঠল–কেন কিছু গন্ডগোল করেছে?
না–তা নয়। আসলে মাঝেমধ্যেই জিগ্যেস করে ওর আমেরিকা থেকে কোনও চিঠি এসেছে কিনা! কিছু আর্জেন্ট চিঠি আসার কথা আছে?
বিতান একটু দ্বিধা করে বলে উঠল,–আসলে ওর বাবা একসময় আমেরিকায় ছিলেন। তাই।
–তা এখনও উনি ওখানেই?
না কয়েকবছর হল–খানিকক্ষণ থেমে বিতান ফের বলে উঠল–ওখানে মারা গেছেন।
চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন মনোহরবাবু। কি বলবেন জানেন না। মৃত্যু তো আসেই। কারোর সময়ে আসে কারোর অসময়ে। কিন্তু বাড়ির রং চটা দেওয়াল–আগাছা ভরা বাড়িতে ঢোকার রাস্তা–আর সর্বোপরি ওই মহিলার মুখ দেখে একটা কথাই মনে হল মনোহরবাবুর। কারো কারো মৃত্যু অনেকসময় এত গভীর দাগ ফেলে যায়, যে সে দাগ আর মোছে না। এখানে যেন তাই জীবনটা শামুকের গতিতে এগোচ্ছে।
মনোহরবাবু আর কথা বাড়ালেন না। বেরিয়ে এলেন। ছেলেটা আবার বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। গ্রিলের রডে নাক ঠেকিয়ে ওনারই দিকে তাকিয়ে আছে।
.
০৫.
–আচ্ছা মা, রাতুল বলছিল এয়ারক্র্যাশ হলেও অনেকে নাকি বেঁচে যায়। ও বলছিল যে যারা প্লেনে বেল্ট বেঁধে বসে থাকে, তাদের নাকি কিছু হয় না। সত্যি মা? ওরা প্লেনে করে ভুটানে বেড়াতে গিয়েছিল। তখন এয়ার হোস্টেস ওকে বলেছে।
হতেও পারে সোনা।
তা হলে মা-বাবাই বলে থেমে যায় পিকু। বিতান কথা বলে না। শুধু পিকুর চুলে আঁকিবুকি কাটতে থাকে। মাথার ওপরে খোলা আকাশ। কিন্তু আজ তারা নেই। সবকটা মেঘের আড়ালে লুকিয়েছে। তবু এই মুখ গোমড়া আকাশের দিকে তাকিয়ে চোখের জলটাকে সামলে নিল বিতান। আজ ওর মন একদম ভালো নেই। আর মন ভালো না থাকলেই ওরা বাড়ির ছাদে চলে আসে। চাওয়া-পাওয়া, আশা-নিরাশার ছোট্টজীবন ওই বিশাল আকাশের কাছে সমর্পণ করে খানিকক্ষণের জন্য শান্তি পাওয়া যায়।
নতুন বছর সবে শুরু হয়েছে। আজ ৩ জানুয়ারি। পরশুদিন সারা শহর যখন নতুন বছরকে বরণের নেশায় উন্মত্ত ছিল, তখন বিতানের একাকীত্ব যেন বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। আশপাশের বাড়িগুলো থেকে ভেসে আসা হাসির আওয়াজ-গান-জোরে কথাবার্তা সবকিছুই যেন অসহ্য লাগছিল। মনে হচ্ছিল সবাই যেন ওদেরকে নিয়েই ঠাট্টা করছে। সবাই যেন ওদেরকে আরও একঘরে করে দিয়েছে। পিকুর উদাস মুখ–মাঝেমধ্যে উদ্দেশ্যহীন ছটফটানি যেন ওই অনুভূতিটাকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল সত্যিই এ-বাড়িতে কিসের যেন বড় অভাব।
আজকে পিকুর স্কুলে অ্যানুয়াল স্পোর্টস ছিল। ওর এখন ক্লাস ফোর হয়েছে। রিলে রেসে সিলেক্টেডও হয়েছিল। কিন্তু হঠাৎ পিকু স্কুলে গিয়ে যে কি ক্ষেপে গেল! কিছুতেই দৌড়বে না। অথচ ও না নামলে ওদের পুরো টিমই দৌড়তে পারবে না। কোনওভাবেই রাজি করানো গেল না পিকুকে। শেষে স্কুল থেকে ওকে শাস্তি দিয়েছে। বেশ খানিকক্ষণ ক্লাসরুমে নিলডাউন করে রেখেছিল। বিতানকেও ক্লাস টিচার ডেকেছিলেন। মাথা হেঁট করে পিকুর সম্পর্কে হাজারো নালিশ শুনতে হয়েছে। ক্লাসে মনোযোগ নেই। কারও সঙ্গে কথা বলে না। কোনও বন্ধু নেই। এমনকী মিস ওর সম্বন্ধে অস্বাভাবিক কথাটা বলতেও ছাড়েননি।
অথচ বিতান জানে যে এসবের পিছনেই আছে ওর বাবার হঠাৎ মৃত্যু। এই তীব্র অভাববোধ সময় সময় ওকে পাগল করে দেয়। আজকেও নিশ্চয়ই খেলার মাঠে প্রায় সবারই বাবাকে সঙ্গে দেখে ওর এই পাগলামি। বিতান জীবনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে চায় বারবার। যে চলে গেছে সে তো আর কখনই আসবে না। কিন্তু পিকুর এই ব্যবহারই ওকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে দেয় না। আরও বেশি করে জয়ন্তর কথা মনে করায়। তাই রাগটা পিকুর ওপরেই প্রকাশ করে বিতান। আজও মাথা এত গরম হয়ে গিয়েছিল যে বাড়িতে এসে বেশ কয়েক ঘা পিকুকে দিয়ে তবেই ঠান্ডা হয়েছে বিতান। তারপরে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে অনেকক্ষণ কেঁদেছে। তারপরে ছাদে উঠে এসেছে। এতসব ঘটনা যেদিন ঘটে যায় সেদিন কি আর খোলা আকাশের নীচে আশ্রয় না নিয়ে ওরা পারে! মনে হয় ওই মেঘের আড়ালেই কোথাও যেন জয়ন্ত আছে। একটা অজানা উষ্ণতা শীতের সন্ধেতেও ছুঁয়ে যায় ওদের। বিতান ছেলের হাতটাকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে নেয়।
২. বাড়ির গ্যারেজে বসে
বাড়ির গ্যারেজে বসে কম্পিউটার মেরামতি করছিল পিকু। ছুটির দিন মানেই বাড়ির বিকল হওয়া যন্ত্রগুলো নিয়ে দিন কাটানো। বেশ লাগে পিকুর। প্রত্যেকটার সঙ্গেই বহুবছরের পরিচয়। শৈশব কৈশোর–পুরোটাই কেটেছে এসব নিয়ে। এদের ছায়াতেই পেরিয়েছে নিঃসঙ্গ দিনগুলো। এক নীরব জগতে এদের সঙ্গেই কথা বলে পিকু কাটিয়েছে এতগুলো বছর। তাই যখনই এদের কোনও একটা সামান্য খারাপ হয়–ডাক্তারি করতে বসে যায় ও।
অপারেশন যে সবসময় সফল হয় তা নয়। তবে অত সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয়। পিকু। তাই গ্যারেজটা হল ওই সব পেশেন্টের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট।
আজকের পেশেন্ট বহুদিনের পুরোনো কম্পিউটার, স্টার্ট হয়েই আপনা থেকে শাট ডাউন হয়ে যায়। এ সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে আজ বাবার কথা খুব মনে হচ্ছে। এই কম্পিউটারেই বাবা কাজ করত। মাঝে কুড়ি বছর পেরিয়ে গেছে। অনেক স্মৃতি অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু বাবার সঙ্গে কাটানো প্রত্যেকটা মুহূর্তের রং আজও ফিকে হয়নি। আজও অনেক রাতে বাবার স্বপ্ন দেখে মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে বসে পিকু। আর ঘুম আসে না। বাবার দেওয়া ছোট ছোট ধাঁধাগুলো চোখের সামনে ভাসে। বলতো সোনা, এই ঘরেই আছে তিন হাত তিন দিকে, শুয়ে থাকে শীতে সুখে।ফ্যান।
তখন না পারলেই বাবার ওপর রাগ করত। তর্ক করত। কিন্তু কীভাবে জানি এসব কিছুই নেশা হয়ে উঠেছিল পিকুর কাছে। স্কুল ফেরত অন্য ছেলেরা যখন ভিডিয়ো গেমস খেলত–ও মজে থাকত ধাঁধায়। মনে হত ধাঁধার ওপারেই দাঁড়িয়ে আছে বাবাই।
এই তো সেদিন একটা শক্ত পরীক্ষার আই কিউ টেস্টের অংশটা দেখে ও আনমনে পুরো দু-ঘণ্টার পরীক্ষাপত্র মাত্র কুড়ি মিনিটে শেষ করে ফেলল। কিন্তু পরীক্ষা দিতে ওর ভালো লাগে না। কেন যেন ওর মনে হয় যে পরীক্ষা মানেই একটা বাঁধন। চারদিক থেকে দাগকাটা একটা মাঠ–তার মধ্যে আরও কয়েকজনের সঙ্গে অহেতুক দৌড়। এই দৌড়ই ওর কোনওদিন ভালো লাগেনি। মনে হয় এই দৌড়ই হয়তো বাবাকে কেড়ে নিয়েছে ওর কাছ থেকে। না হলে তো বেশ ছিল লুডোর বোর্ডের দুনিয়া। হার-জিত হয়, কিন্তু বারবার শুরু করা যায় শুরু থেকে।
এত বছর হয়ে গেছে, এখনও বাবার পড়ার ঘরে যেতে ওর খুব খারাপ লাগে। ওঘরে সার দিয়ে বইয়ের আলমারি, নানান ধরনের বই। বাবার ছুটির দিনের অনেকটা সময় জুড়ে থাকত বই। আর ছোট্ট পিকু উঁকিঝুঁকি মারত দরজার ফাঁক দিয়ে। ভারি রাগ হত বইগুলোর ওপর। বাবার সঙ্গে খেলার সময়টা কেড়ে নিচ্ছে ওরা।
বাবা পিকুকে বলত, বুঝলি পিকু, এসব বই তোর জন্য। বড় হয়ে পড়বি। দেখবি এদের জগৎ একেবারে আলাদা। এ জগতে ঢুকতে গেলে শুধু মনের দরজাটা খুলে রাখতে হয়। এরা তখন তোর সঙ্গে কথা বলবে, আর বলে দেবে কীভাবে সত্যিকারের মানুষ হতে হয়।
দাদাবাবু, ঘর পরিষ্কার করতে গিয়ে এ লুডোটা পেলাম–ফেলে দেব? চাকর গণেশের কথায় হুঁশ ফিরল পিকুর।
গণেশ ঘর পরিষ্কার করে। ওকে আজকে বাবার পড়ার ঘরটা পরিষ্কার করতে বলেছিল পিকু।
কই দেখি!
–আলমারির পিছনে পড়ে গিয়েছিল। কী নোংরা যে হয়েছিল ঘরটা!
লুড়োটা হাতে নিয়েই চোখে জল এল পিকুর। কুড়ি বছর আগে কত দিন কেটেছে এই লুডো নিয়ে।
না, ফেলো না। বলে লুডোর পাতা ওলটাল পিকু। সাপলুডোর পাতাটা দেখে মনে হল কতবার দান ফেরত নিত। সাপ পড়লে চলবে না। সিঁড়ি মিস করলে চলবে না। বায়না করে ঠিক আদায় করে নিত। জীবনের সাপলুডোতেও যদি একইভাবে বায়না করে বাবার কয়েকটা দিন আরও আদায় করা যেত!
সাপলুডোর 4 আর 18–ওই নাম্বার দুটোতে ক্ৰশ। লাল পেনসিলের দাগ। লুডোটা হাত থেকে নামিয়েই রাখছিল পিকু, হঠাৎ একটা কথা খেয়াল হতেই প্রচণ্ড উত্তেজিত হয়ে পড়ল।
বাবার আমেরিকা যাওয়ার কয়েকদিন আগের কথা। সেদিন বাবা অফিস থেকে ফিরে এসে অফিসের পোশাকেই পিকুর সঙ্গে লুডো খেলছে। হঠাৎ একটা ফোন এল। বাবা উঠে অন্য ঘরে চলে গেল। খানিকবাদে ফিরে এল। সেদিন বাবা বারবার খুব অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। বারবার পিকুর মাথায় হাত রেখে আদর করছিল। আর স্পষ্ট মনে আছে ওই দুটো বক্সে বাবা পিকুর পেনসিল দিয়ে ক্রস করে বলেছিল, কী বলত এটা পিকু?
তারপর একটু থেমে ভারী গম্ভীর গলায় বলেছিল,–দুটো সাপ–যাদের আমি কখনও ডিঙোতে পারব না।
পিকু তখন সংখ্যা ভালো চিনত না, সাপ চিনত। তাই অদৃশ্য সাপের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে ছিল খানিকক্ষণ। আর আজ খুব অবাক লাগছে যে ওই সংখ্যাদুটো পাশাপাশি বসালে যেটা হয় সেটা হল বাবার মৃত্যুদিন। 14 এপ্রিল। 2002 সালের এই দিনেই বাবার এয়ার ক্র্যাশ হয়। এটা শুধুই কোইনসিডেন্স? হঠাৎ করে মিলে যাওয়া?
গ্যারেজ থেকে ওপরে উঠে এল পিকু। সারা বাড়িটাই খুব অগোছালো অবস্থায় আছে। দু-বছর আগে মা মারা যাওয়ার পর থেকেই বাড়িটা গণেশের ওপর থাকে।
ড্রয়িংরুম পেরিয়ে বাবার পড়ার ঘরে ঢুকল পিকু। অনেকদিন এঘরে ঢোকেনি ও। বুককেসের ভেতরে সারি সারি বই। নীচের তাকে বাবার অনেক খাতাপত্র, ফাইল। সময়ের দাগ পড়েছে সেসব কাগজে। লাল হয়ে উঠেছে। বাবা নিয়মিত ডায়েরি ফলো করত। পরপর সাজানো ডায়েরিগুলো। প্রত্যেক বছরের ডায়েরি খুলে ভালো করে দেখল পিকু। নাহ, কিছুই তেমন চোখে পড়ল না।
বাবা মারা যায় ১৪ এপ্রিল 2002। তার কয়েকদিন আগে ডায়েরির পাতায় ডঃ ডেভ জর্ডন বলে একজনের নাম লেখা। অ্যাড্রেসও আছে। অ্যানআবার শহরের ঠিকানা। একটা ফোন নাম্বারও লেখা। কী ভেবে পিকু ওই নাম্বারে ফোন করল। রং নাম্বার, খুবই স্বাভাবিক। কুড়ি বছরে মানুষই পালটে যায়, ফোন নাম্বার তো পালটাবেই।
কাগজপত্রের মধ্যে থেকে পিকুর ছোটবেলাকার একটা ছবি বেরোল। তিন-চার বছর বয়সের ছবি। কবে তোলা কিছু মনে নেই। ফোটোটা বার করে টেবিলের ওপর রাখল পিকু। তারপর কী মনে হতে আবার হাতে তুলে নিল। এটা কি ওরই ছবি! চোখের পাশে কাটা দাগটা কীসের? ওখানে তো কোনওদিন পিকু চোট পায়নি। আর ছবিটা সাদা কালো কেন? ওর সব ছবিই তো কালার্ড। ছোটবেলারও। আর ছবিটা দেখে মনে হয় না ভারতে তোলা। পিছনে সার দিয়ে পাম গাছ।
খানিক ভেবে অরিন্দমকাকুর নাম্বারটা বের করে ফোন করে পিকু। অরিন্দমকাকু বাবার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ওনার সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার।
.
০৭.
–কী খবর? এতদিন বাদে পিকু সাহেবের ফোন?
কাকু একটা জরুরি দরকারে তোমাকে ফোন করছি।
–হ্যাঁ, কী ব্যাপার বল।
–শোনো, আমি সেদিন একটা পুরোনো লুডো খুঁজে পেয়েছি। এটা আমি আর বাবাই। একসঙ্গে বসে খেলতাম। বহু বছর আগে। বাবাই আমেরিকা যাওয়ার দুদিন আগেও খেলেছি। ওই লুডোর বোর্ডে দুটো সংখ্যা মার্ক করা ছিল, আর সেটা হল বাবার মৃত্যুদিন।
আশ্চর্য! তা তোর কী মনে হয়? পরে কেউ ওই বোর্ডে মার্ক করতে পারে?
না, তার সম্ভাবনা খুব কম। বাবাই-এর মারা যাওয়ার খবরটা পেয়ে আমি রেগে ওই লুডোটা বইয়ের আলমারির পেছনে ফেলে দিয়েছিলাম। তারপর ভুলেও গিয়েছিলাম। এতদিন বাদে ঠিক ওই জায়গাতেই লুডোটা পাওয়া গেছে। অর্থাৎ কারও ওই লুডোতে হাত দেওয়া সম্ভব ছিল না।
–তাহলে কী হতে পারে? কোনওভাবে মিলে গেছে।
আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে। বাবাই আর আমি খেলছিলাম–একটা ফোন এল। বোধহয় বাইরের ফোন। আমার মনে হয়, তখনই বাবাই ওটা লেখে।
–তাহলে কী হতে পারে? এটা তো কোনওভাবেই এক্সপ্লেন করা যাচ্ছে না। তবে তুই বললি বলে মনে পড়ল। তোর বাবা তো প্রায়ই বাইরে যেত। তা সেবারে যাওয়ার আগে কেন জানি আমার কাছে এল। সন্ধেবেলা–আমি সবে অফিস থেকে ফিরেছি। কথায় কথায় বলল, তোর আর তোর মার ওপর যেন খেয়াল রাখি। আর কোথায় কোথায় ওর ফিক্সড ডিপোজিট, ইনসিওরেন্স আছে, তার ডিটেলসের একটা প্রিন্ট আউটও নিয়ে এসেছিল। তাহলে কি ও টের পেয়েছিল যে ওর মৃত্যু হতে পারে–কে জানে?
–এটাও তো হতে পারে যে ওটা কোনও প্ল্যানড মার্ডার। বাবাইকে কোনও ঘটনার শিকার হতে হয়েছিল। বাবাই কোনওভাবে জানতেন ঘটনাটা ওই দিনেই হবে। আচ্ছা কাকু, বাবাই-এর অফিসে গিয়ে একবার খোঁজ নিলে কেমন হয়?
–ঠিক বলেছিস। তুই বড় হয়েছিস, তাই তোকে বলি। তোর বাবা আমার খুব বন্ধু ছিল বটে, কিন্তু আমরা তো স্কুলের বন্ধু। ওর কোনও অফিসের বন্ধু সেরকম ছিল না। শুধু তাই নয়, ও অফিসের ব্যাপারে কোনও কথাই প্রায় বলত না। শুধু জানতাম যে ও ইনোভেটিভ সলুশনস-এ কাজ করে।
–আচ্ছা কাকু, আমার কি কোনও দাদা ছিল, ঠিক আমারই মতো দেখতে?
কী আবোল তাবোল বলছিস! দাদা থাকলে তুই জানবি না? আমি জানব না? কেন, হঠাৎ করে মনে হল কেন?
–আমার কেন জানি না, ছোটবেলা থেকেই মনে হত যে আমার সঙ্গে কারও অদৃশ্য প্রতিযোগিতা চলছে। কমপ্যারিসন। বিশেষ করে মার কথায়। হয়তো খাচ্ছি মা হঠাৎ বাবাইকে বলে উঠত দ্যাখো ঠিক ওর মতো খাবার ধরন। মুখে খাবার টোপলা করে রেখে দেয়। অথবা হয়তো বাবার সঙ্গে খেলছি, বাবা বলে উঠত–এ-ও দেখবে, খুব ইনটেলিজেন্ট হবে। কীরকম চটপট ধাঁধাগুলোর উত্তর দিচ্ছে দেখছ। একমাত্র ও ছাড়া আর কাউকে এরকম চটপট উত্তর দিতে দেখিনি।
–তা তোর হঠাৎ করে একথা খেয়াল হল কেন?
কাল আমি একটা ছবি পেয়েছি। বাবার লেখার আলমারি থেকে। চট করে দেখলে মনে হবে আমার ছবি। কিন্তু পরে খুঁটিয়ে দেখে মনে হয়েছে ওটা আমার নয়। একই বয়সের আমার ছবির খুব কাছাকাছি কিন্তু আমি নই।
ভারতে ফেরার আগে তোর বাবা প্রায় বারো বছর আমেরিকাতে ছিল। তখন আমার সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ ছিল না। তবে…।
কী, কাকু? তবে কী? মনে হচ্ছে তুমি আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছ। কাল ওই ছবিটা পাওয়ার পরে অনেক খোঁজাখুঁজি করি। একটা পুরোনো অ্যালবামে আরও কিছু ছবি পাই। ওই ছেলেটারই। ছবিগুলো বিদেশের। দেখেই বোঝা যায়। আমি তো কখনও বিদেশেই যাইনি। তুমি লুকিও না কাকু, আমার জানা দরকার, হয়তো বাবার মৃত্যু আর এটা রিলেটেড।
খানিকক্ষণ চুপ থেকে অরিন্দম বলে,–জেনেই যখন গেছিস–তখন বলছি। তোর বাবা আর মাকে কথা দিয়েছিলাম যে এ ব্যাপারে আমি তোকে কোনওদিন কিছু জানাব না। হ্যাঁ, তোর এক দাদা ছিল। বছর পাঁচেক বয়সে মারা যায়। এটা আমেরিকাতে থাকাকালীন হয়। আমি কখনও তাকে দেখিওনি।
–আমি তাহলে একইরকম দেখতে হলাম কী করে?
–সেটা জানি না। আমি তাকে দেখিওনি। এ রহস্যটা উদ্ধার করতে হবে।
.
০৮.
স্যার, একটা ছেলে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।
–কেন?
–ওর বাবা জয়ন্ত চ্যাটার্জি নাকি আমাদের কোম্পানিতে কাজ করত কুড়ি বছর আগে। কিন্তু আমরা কোম্পানি রেকর্ডে কোথাও পাইনি।
–রেকর্ড ভালো করে দেখেছ?
–হ্যাঁ। ছেলেটা বেশ কয়েকদিন ঘোরাঘুরি করছে। ওর বাবা কুড়ি বছর আগে মারা যান। আমাদের কোম্পানির কাজে আমেরিকায় গিয়ে। মারা যান 2002-এ। এয়ার ক্র্যাশে।
–2002-তে তো আমিও ছিলাম। ওরকম কোনও ইনসিডেন্ট তো মনে পড়ছে না।
–হ্যাঁ, স্যার আমিও আমাদের সব রেকর্ড দেখেছি। এরকম কোনও এমপ্লয়ির মারা যাওয়ার কথা কোথাও নেই।
–তা ছেলেটা কুড়ি বছর বাদে এসেছে কেন? দাবিদাওয়া নিয়ে?
না, না, ছেলেটার কোনও দাবিদাওয়া নেই। এমনকী বলেছে যে আমাদের কোম্পানির থেকে ভালোরকম কমপেনসেশনও নাকি পেয়েছে। তা না হলে ওদের সংসারই চলত না।
ইন্টারেস্টিং! পাঠাও তো ছেলেটাকে। দেখি কথা বলে। তুমিও থাকো। বললেন, মি. বসি। উনি ইনোভেটিভ সলিউশনসের ইস্টার্ন রিজিয়নের হেড। ইনোভেটিভ সলিউশনস এখন সারা পৃথিবীর প্রথম দশটা আইটি কোম্পানির মধ্যে পড়ে। তবে কুড়ি বছর আগে সেরকম ছিল না। তখন মোটে হাজার দুয়েক কর্মী ছিল। একজন আরেকজনকে ভালোরকম চিনত।
মিঃ বকসির চেম্বারে ওনার সেক্রেটারি সীমার সঙ্গে একজন ছেলে এসে ঢুকল।
বসার সিট দেখিয়ে মিঃ বকসি ছেলেটার দিকে তাকালেন। চেহারার মধ্যে সম্ভ্রান্ত বংশের ছাপ। চোখদুটো খুব উজ্জ্বল। চশমাতেও সেই ঔজ্জ্বল্য ঢাকা পড়েনি। একটু যেন অস্থিরতার ভাব। হাতে একটা ফাইল। টেবিলের ওপর ফাইলটা রেখে একটা চিঠি বার করে মিঃ বকসির দিকে এগিয়ে দিল।
অতবছর আগের সব চিঠিপত্র নেই, তবে পুরোনো কাগজপত্র ঘেঁটে একটা চিঠি। পেলাম।
–দেখি–! মিঃ বকসি অভিজ্ঞ চোখে চিঠিটাতে চোখ বোলালেন। ইনোভেটিভ সলিউশনসের লেটার হেডে। জয়ন্তর মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট চিঠি দিয়েছেন। জানিয়েছেন দশ লাখ টাকা অর্থ সাহায্যের কথা। কিন্তু যার নাম সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে উল্লিখিত, সেই এন নরসিহন–নাহ্, মিঃ বকসি নামটা খেয়াল করতে পারলেন না।
–এই চিঠিটা রাখতে পারি? আমাদের একটু সময় দিতে হবে। দু-তিন দিনের মধ্যে চিঠিটা আসল না নকল তা বলে দিতে পারব।
–বুঝলাম না, আপনার কি মনে হয় চিঠিটা আসল নয়?
এমনিতে সন্দেহ করার কিছু নেই। তবে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট বলে যার নাম আছে, সেই এন নরসিমহন বলে কেউ ছিলেন না। তবু আমরা আমাদের সব রেকর্ড দেখব। তা, তোমার বাবার ছবি, পাসপোর্ট এসব কিছু আছে?
–হ্যাঁ, বলে এগিয়ে দিল পিকু, তবে বাবা তো সঙ্গে করে পাসপোর্ট নিয়ে গিয়েছিলেন। অনেক খুঁজে পাসপোর্ট-এর প্রথম দুটো পাতার কপি পেয়েছি। আপনি এটাও রাখতে পারেন। আমার কাছে কপি আছে।
–গুড! মিঃ বকসি একটু থামলেন। তিরিশবছরের চাকরিতে অনেক কিছু দেখেছেন, কিন্তু এরকম ঘটনা কখনও হয়নি। ডিটেকটিভের ভূমিকায় নিজেকে ভেবে নিয়ে বললেন, তা তোমার বাবার কোনও বন্ধু ছিল না? এ অফিসের কারও নাম জানতে?
–না, আসলে আমি তখন খুব ছোট ছিলাম। মা-ও মারা গেছেন দু-বছর হল। বাবার এক স্কুলের বন্ধুর সঙ্গে কথা বললাম, উনিও কিছু বলতে পারলেন না।
–আশ্চর্য! ঠিক আছে চিন্তা কোরো না। আমরা দু-তিন দিনের মধ্যেই জানিয়ে দেব যে উনি আমাদের অফিসে কাজ করতেন কিনা।
ধন্যবাদ জানিয়ে পিকু মিঃ বকসির চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল।
পিকু বেরোনোর পর মিঃ বকসি সেক্রেটারিকে একবার ডেকে নিলেন।
সীমা, ছেলেটাকে সবরকমভাবে সাপোর্ট করো, আমি নিশ্চিত যে চিঠিটা জাল। কিন্তু প্রশ্নটা হল হুবহু কোম্পানির লেটারহেডে কে চিঠি লিখল, আর কেই বা কমপেনসেশন পাঠাল? আর এন নরসিহন-ই বা কে? এমপ্লয়ি ডেটাবেসের সঙ্গে ছেলেটির বাবার ছবিটাও মিলিয়ে নিও।
.
০৯.
জীবনটা কোনওদিনই খুব সহজভাবে ধরা দেয়নি পিকুর কাছে। খুব হিংসে হত যখন স্কুলে দেখত অন্য ছেলেরা বাবার হাত ধরে যাচ্ছে। মনে হত ম্যাজিকের মতো যদি ওর বাবাও এসে হাজির। হত! এত বছরে ব্যাপারটা অবশ্য খানিকটা মেনে নিয়েছিল। কিন্তু গত কয়েকদিনে জীবন যেন ওকে নিয়ে ফের ঠাট্টা করতে শুরু করেছে। একের পর এক অচেনা তথ্য সামনে এসে জড়ো হয়েছে।
ইনোভেটিভ সলিউশনস থেকে মিঃ বকসি ফোন করেছিলেন দুদিন বাদে। জয়ন্ত চ্যাটার্জি বলে কোনও সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার কোনওকালে ওই কোম্পানিতে কাজ করেনি। চিঠিটাও ভুয়ো। তাহলে প্রশ্ন, তখন অত টাকা পাঠাল কে? ওই টাকা না পেলে ওদের সংসারও চলত না।
অনেকদিন আগের কথা। ব্যাঙ্কে খোঁজ নিয়েও কিছু জানা যায়নি।
এসব নিয়ে পিকু ভাবছে, হঠাৎ কলিংবেল বাজল। ক্যামেরায় পিকু দেখতে পেল বাইরে। অরিন্দমকাকু। সঙ্গে সঙ্গে রিমোটে দরজা খুলে দরজার দিকে এগিয়ে গেল পিকু। ঢোলা প্যান্ট, আগেকার দিনের চশমা আর ছাতা, অরিন্দমকাকুকে দেখলেই মনে হয় সময় যেন আর এগোয়নি। সেই কুড়ি বছর পিছিয়ে আছে। সবসময় মুখে হাসি।
পিকুর পিঠে চাপড় মেরে সোফার দিকে এগিয়ে গেলেন অরিন্দমকাকু।
বুঝলি পিকু, আরেকটা ইন্টারেস্টিং খবর চোখে পড়ল। বলে একটা পুরোনো খবরের কাগজ এগিয়ে দিলেন। নিউইয়র্ক টাইমস। 1998, 17 জুলাই। লাইব্রেরির আর্কাইভ ঘাঁটতে গিয়ে চোখে পড়ল। ছবিটা দ্যাখ।
–একী! এ তো বাবার ছবি!
–হ্যাঁ, জয়ন্তর ছবি। শুধু তাই নয়, যাদের সঙ্গে ছবি তোলা তারা প্রত্যেকেই বিখ্যাত জেনেটিক সায়েন্টিস্ট। ছবিটা অ্যান আবারে, ইউনির্ভাসিটি অফ মিসিগানে তোলা। সঙ্গের লেখাটা পড়। জেনোম রিসার্চে যে টিম কাজ করছিল তার ছবি নাকি এটা।
–আশ্চর্য, বাবার তো অন্য প্রফেশন–উনি জিন-এর রিসার্চের সঙ্গে যুক্ত হলেন কী করে?
–আমিও তাই ভাবছি। জয়ন্ত খুবই ব্রিলিয়ান্ট ছেলে ছিল। তখনকার দিনে আমাদের বোর্ডের টপার। প্রচণ্ড হাই আই কিউ ছিল। তা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার পর ও যখন মাস্টার্স করতে বিদেশে গেল, তখন ওর সাবজেক্ট কী ছিল তা আমার জানা নেই। তারপর তো ও ওখানে ডক্টরেটও করেছিল। ও এসব নিয়ে কখনও আলোচনা করত না।
একটু থেমে অরিন্দমকাকু আবার বললেন, আমি বলি কি পিকু, এখানে বসে না থেকে আমেরিকায় চলে যা। যা কিছু ঘটেছে, সবই তো ওখানে।
–কিন্তু আমেরিকা তো একটা বিশাল দেশ। যাব কোথায়?
–কেন? তুই ইউনিভার্সিটি অফ মিসিগান দিয়েই শুরু কর। অর্থাৎ ডেট্রয়েট–অ্যান আবার। ওখানে নিশ্চয়ই কোনও সূত্র পাবি। আর আমার এক বন্ধু সুবীর রায় ওখানেই থাকেন। তুই ওখানেই গিয়ে উঠতে পারিস। তবে
তবে কী কাকু?
নাহ্, সে তেমন কিছু নয়। তবে সুবীরের ছেলে পিলে হয়নি। স্ত্রী-ও মারা গেছেন। একটু বেশি কথা বলে। আর
–আর, আর কী?
বাঙালির যা অভ্যেস, একটু বাড়িয়ে বলে। হেসে উঠলেন অরিন্দমকাকু।
.
১০.
কলকাতা থেকে দুবাই। দুবাই থেকে ডেট্রয়েট। আজকালকার দিনে প্রায় সবাই ছোটবেলা থেকেই প্লেনে চড়ে। পিকুর অবশ্য এবারই প্রথম। আর প্রথমবারেই এতটা পথ। তাই সময় যেন কাটতেই চাইছিল না।
ডেট্রয়েট যখন পৌঁছোল তখন ওখানে সন্ধে। ইমিগ্রেশনের বিশাল লাইন। তবে খুব সুন্দরভাবে পরিচালনা করায় বেশ তাড়াতাড়ি লাইন থেকে বেরিয়ে গেল।
লাগেজ নিয়ে এয়ারপোর্টের বাইরে বেরিয়ে ফোন করল সুবীর রায়কে। এয়ারপোর্টের কাছেই গাড়ি পার্ক করে উনি পিকুর ফোনের অপেক্ষা করছিলেন। মিনিট দশেক বাদে পিকু দেখল অদ্ভুত সবুজ রঙের একটা বিশাল গাড়ি ওর দিকে এগিয়ে আসছে। গাড়ি থামতে এগিয়ে গেল পিকু। ভদ্রলোক দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন।
–পিকু?
–হ্যাঁ।
–আরে আমি অনেকক্ষণ এসে গেছি। ভাবলাম ফ্লাইট যদি আগে পৌঁছে যায়। নাও, গাড়িতে ওঠো, আমার বাড়িটা অ্যান আবারের নর্থ-ওয়েস্ট সাবার্বে। পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মতো লাগবে।
–তা আপনি তো এখানে বহুদিন আছেন, আমার বাবাকে চিনতেন না? জয়ন্ত চ্যাটার্জি।
–না, আসলে আমার তো এখানে ব্যবসা। আগে সানফ্রান্সিসকোতে ছিলাম।
একটু থেমে সুবীরবাবু বলে উঠলেন, তোমার বাবা তো এয়ার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গিয়েছিলেন, তাই না?
–হ্যাঁ, আমেরিকান এয়ারলাইনস। 2002-এর 18 এপ্রিল।
–আমার মনে আছে ইনসিডেন্টটা। প্লেনটা ভেঙে পড়ে ডেট্রয়েট থেকে দুশো মাইল দূরে। চুপ করে গেলেন সুবীর রায়।
পাশে পিকু জানলার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। পিকুর উদাসীন হওয়ার কারণটা বুঝতে পেরে ফের বলে উঠলেন, বুঝলে, আমার দারুণ লাগছে। এতদিন বাদে বাড়িতে একজন বাঙালি অতিথি। এক সময় তবু বন্ধু-বান্ধবদের যাতায়াত ছিল। এখন সবাই ভিডিয়ো ফোনে খোঁজ নেয়। কেউ আর আরেকজনের বাড়ি যায় না। আমার বাড়িটা বিশাল। লাগোয়া বাগানটাও বেশ বড়। ওখানে শয়ে শয়ে হরিণ আসে। লুকোচুরি খেলে।
বলেই পিকুর অবাক চোখের দিকে তাকালেন, শখানেক না হলেও দু-তিনটে রেগুলার আসে। তা যা বলছিলাম, তুমি কি এখানে কোনও কাজে এসেছ?
–হ্যাঁ, আমি আমার রিসার্চ সংক্রান্ত কিছু কাজ নিয়ে এসেছি। তাছাড়া বাবা তো এখানেই মারা গিয়েছিলেন, তাই জায়গাটা দেখার ইচ্ছে আছে। বাবার শেষ দিকের রিসার্চ নিয়েও একটু খোঁজ খবর নেব।
অরিন্দমকাকু পিকুকে আগেই বলে রেখেছিলেন আসার আসল কারণটা সুবীর রায়কে আসামাত্রই না বলতে। সাদাসিধে লোক–অহেতুক সবাইকে বলে বেড়াবেন। আপাতত গাড়ি ইন্টারস্টেট রাস্তার ওপর দিয়ে যাচ্ছে। পাশে একটা গাড়িকে পুলিশ ধরেছে। রোবট পুলিশ। সাইডে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়েছে।
ওদিকে তাকিয়ে সুবীরবাবু বলে উঠলেন,–এদের চোখ এড়ানোর উপায় নেই। একটু নিয়ম ভাঙলেই ফলো করে এসে ঠিক ধরবে। আজকাল আমেরিকায় এ ধরনের রুটিন কাজে মানুষের বদলে রোবট ব্যবহার করা হচ্ছে।
–বলে একবার আড়চোখে তাকালেন পিকুর দিকে। ফের বলতে শুরু করলেন,–তা বলে এদের হাবাগোবা ভেবো না। ওরকম পিটপিটে চোখ, বোকা বোকা চেহারা হলে কি হবে! আইনজ্ঞান টনটনে। কয়েকদিন আগে একটা স্টেট হাইওয়ে দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ মনে হল আমার। পুরোনো এক বন্ধু কল্যাণ যেন উলটোদিকে গাড়ি চালিয়ে চলে গেল। ওর সঙ্গে আমার বহুদিন যোগাযোগ নেই। তাই টুক করে গাড়ি ঘোরালাম। যেখানে ঘোরালাম, সেখানে ঘোরানোটা নিষিদ্ধ। কিন্তু কলকাতার অভ্যেস যাবে কোথায়! যেই ঘুরিয়েছি দেখি সাইরেন বাজিয়ে এক পুলিশের গাড়ি হাজির। একটা বড় রকমের ফাইন। তা সে না হয় দিলাম। মনে হল রোবট পুলিশটার সঙ্গে একটু আড্ডা মারি। বন্ধু হারিয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে যদি মেটানো যায়। বুঝিয়ে বলি কী জন্য ঘোরালাম। বন্ধুদের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে একটু বোঝাই। আজকের দিনে স্কুলের বন্ধুর সঙ্গে হঠাৎ করে রাস্তায় দেখা পাওয়া কতটা ভাগ্যের ব্যাপার। ভালোরকম বোঝালাম। দেখি খুব মনোযোগ দিয়ে শুনল। বারদুয়েক থ্যাংক-ইউ ও বলল। তারপর দেখি আবার ফাইন করেছে। এবারের কারণ ওর অহেতুক সময় নষ্ট করা। বোঝো!
ঠিক পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগল। সুবীর রায়ের বাড়িটা বেশ ফাঁকা জায়গায়। শহরের একটা প্রান্তে। দেখেই বোঝা যায় বেশ উচ্চবিত্তদের পাড়া। বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে বাড়িটা। গ্যারেজে গাড়ি পার্ক করে সিকিওরিটি কোড দিয়ে দরজা খুলে বাড়ির ভেতরে ঢুকল ওরা।
৩. ডিজিটাল কপি আর্কাইভ
এখানে একটা বড় সুবিধে হল সব ইনফরমেশনই চট করে খুঁজে পাওয়া যায়। অ্যান আবারের লাইব্রেরিতে 2002-এর 19 এপ্রিলের খবরের কাগজটা খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না। ডিজিটাল কপি আর্কাইভ করা ছিল। সেটাতে চোখ বোলাল পিকু।
নিউইয়র্ক থেকে ডেট্রয়েট যাচ্ছিল আমেরিকান এয়ারলাইনসের ফ্লাইট E120। তিরিশ জন যাত্রী ছিল তাতে। বেশিরভাগই বিজ্ঞানী। জেনেটিক সায়েন্সের ওপর এক কনফারেন্সের পর ডেট্রয়েট ফিরছিলেন তারা। পথে প্লেন দুর্ঘটনা হয়–সকাল সাড়ে ছটার সময়। ডেডবডিগুলো সনাক্ত করা যায়নি। নামের লিস্ট আছে–চোখ বোলাতেই তাতে ঝাপসা চোখের সামনে জয়ন্ত চ্যাটার্জির নামটা দেখতে পেল পিকু। খবরটা তাহলে মিথ্যে নয়। অন্যান্য যাত্রীর নামের মধ্যে আরেকটা পরিচিত নাম পেল পিকু। ডেভ জর্ডন। এরই নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার, বাবার ডায়েরিতে পেয়েছিল পিকু।
আচ্ছা, এই নাম-অ্যাড্রেস তো পিকুর কাছেই আছে। বাড়িটা যখন অ্যান আবারে, যাওয়াটা শক্ত কিছু নয়। একবার গিয়ে খোঁজ নেবে কি?
হয়তো ডেভ জর্ডনের পরিবারের কেউ এখনও ওখানে থাকেন। হয়তো বাবার সম্বন্ধেও কিছু বলতে পারবে।
পরের দিন কাগজটা খুলল পিকু। 20 এপ্রিল 2002। ক্র্যাশের খবরটা নিউইয়র্ক টাইমসের প্রথম পাতা জুড়ে। ক্র্যাশসাইটের কয়েকটা টুকরো ছবি। প্লেনের ছোট ছোট কয়েকটা টুকরো। একটা আধপোড়া জুতো। এ ধরনের প্লেনে আগে কখনও এরকম বিপর্যয় ঘটেনি। প্রাথমিকভাবে যেভাবে হঠাৎ করে ভেঙে পড়েছে তা দেখে অনুমান করা হচ্ছে বিমানে কোনও বিস্ফোরণ হয়েছিল। ডেটা রেকর্ডার–ভয়েস রেকর্ডার খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে। টেররিস্টদের হাত থাকলেও থাকতে পারে।
22 এপ্রিলের কাগজের দ্বিতীয় পাতায় বড় করে বিমান দুর্ঘটনার প্রতিবেদন। তাতে প্লেনের সব যাত্রীদের ছবিও আছে। বাবারও ছবি আছে দ্বিতীয় সারিতে। চুপ করে ছবিটার দিকে তাকিয়ে রইল পিকু। কত আপনজন একমুহূর্তে কত দূরে চলে যায়। বাবার মুখে সেই ছেলেমানুষি হাসি। তাহলে খবরটায় কোনও ভুল নেই। অন্তত প্লেন অ্যাক্সিডেন্টে বাবার মৃত্যু নিয়ে কোনও রহস্য নেই। তবু–তবু কেন পিকুর আজও মনে হয় সব তথ্য ভুল। আজও মনে হয় মানুষটা সামনেই জলজ্যান্ত দাঁড়িয়ে আছে।
আরেকটা কথা খেয়াল হল, বাবার পাসপোর্ট নাম্বার আর আমেরিকার স্যোশাল সিকিওরিটি নাম্বার তো পিকুর কাছেই আছে। তার থেকেও যদি কিছু সূত্র পাওয়া যায়। গত কয়েকবছর আমেরিকাতে প্রত্যেকের বায়োমেট্রিক আইডেনটিফিকেশনের জন্য কার্ড চালু হয়ে গেছে। কিন্তু আগের স্যোশাল সিকিওরিটি নাম্বার দিয়েও যে কারও সব তথ্য খুঁজে বের করা যায়।
পিকু ইন্টারনেটে সার্চ করল ওই নাম্বার ধরে। ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করে এরকম একটা বিশেষ সংস্থা ওই নাম্বারের ওপর নির্ভর করে কোনও ব্যক্তির যাবতীয় তথ্য সামান্য চার্জের বিনিময়ে জানিয়ে দেয়। তাতে সার্চ করতে জয়ন্ত চ্যাটার্জির আমেরিকায় থাকার যাবতীয় ইতিহাস চট করে পেয়ে গেল পিকু। 86 থেকে 93 বস্টন। দুটো ডিফারেন্ট অ্যাড্রেস। তারপর 93 থেকে 97 ডেনভার কলোরাডোতে। 97-এর শেষের দিকে কলকাতায়।
কিন্তু এসব অ্যাড্রেসের বাইরেও আরেকটা অ্যাড্রেস দেখাচ্ছে জয়ন্ত চ্যাটার্জির নামের সঙ্গে। 91 থেকে 2002। আর সেটা অ্যান আবারের অ্যাড্রেস, অর্থাৎ যেখানে পিকু এখন আছে।
অ্যান আর্বারে বাবার থাকার কী কারণ? আর তা কেউ জানত না কেন? দ্রুত ওই অ্যাড্রেসটা নোট করে নিল পিকু।
আর মিনিট পাঁচেক বাদে পিকু লাইব্রেরি থেকে বেরিয়ে এল। সুবীরবাবু বাইরে অপেক্ষা করছেন।
কী কাকু, আপনি ভেতরে এলেন না কেন?
এসেছিলাম বাবা। একজনের সঙ্গে একটু আলাপ করছিলাম। লোকটাকে আমার চেনা। চেনা মনে হচ্ছিল। জিগ্যেস করছিলাম কোথায় থাকে, কী করে ইত্যাদি। তারপর সুপারবোল খেলা, আজকের ওয়েদার এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলছি, হঠাৎ দেখি লাইব্রেরির সিকিউরিটি এগিয়ে আসছে। কথা বলা বারণ। তাই আমাকে নাকি বাইরে বেরিয়ে কথা বলতে হবে। বোঝো! লোকটাকেও আসতে বললাম বাইরে। তা তার নাকি ভেতরেই একটু কাজ আছে। এলো না। অগত্যা একা দাঁড়িয়ে। যত সব নিয়ম! তা এবার কোথায় যাবে?
–এই অ্যাড্রেসটায় যেতে পারলে ভালো হত। তা এখন আপনার সময় হবে কি?
কীসের অ্যাড্রেস?
বাবা কোনও একটা সময়ে ওই ঠিকানায় ছিলেন। ইন্টারনেটে পেলাম। অ্যান আবারেই। তাই ভাবলাম যদি যাওয়া যায়।
–আরে অবশ্যই, এখনই চলো।
সুবীর বাবুর ফোর্ড গাড়িতে উঠে বসল পিকু। উনি ধারাভাষ্য শুরু করলেন, বুঝলে পিকু, অ্যান আবার কিন্তু খুব পুরোনো শহর। মিসিগান ইউনিভার্সিটির বয়সই তো কয়েক হাজার বছর।
বলে পাশে বসা পিকুর মুখের হাসিটা দেখে বলে উঠলেন,–আহা, দুশো বছর কি কম হল! 1817 সালে মিসিগান ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানকার ইঞ্জিনিয়ারিং, সারা বিশ্বের সেরা।…
জিপিএস অনুযায়ী গাড়ি ছুটে চলল অ্যান আবারের রাস্তা ধরে। ইউনিভার্সিটি, মিসিগান হসপিটাল পেছনে ফেলে গাড়ি এগিয়ে চলল দক্ষিণ শহরতলীর দিকে। প্রায় আধঘণ্টা বাদে একটা মাটির রাস্তায় এসে পড়ল ওরা। প্রাইভেটলি মেনটেন্ড রাস্তা। ধারে সাইনবোর্ডে লেখা দেখে বোঝা গেল যে হরিণ যে-কোনও সময়ে রাস্তা পেরোতে পারে। বাঁদিক-ডানদিকে বেশ খোলা খোলা মাঠ, ভুট্টাখেত। একটা বড় খামারবাড়ির সামনে এসে গাড়ি দাঁড় করালেন সুবীরবাবু।
–এসে গেছি। দুম করে ঢুকো না। ট্রেসপাসিং হবে। বাড়ির লোক সেরকম সহৃদয় না হলে গুলিও চালাতে পারে।
অগত্যা দূরে থেকেই অপেক্ষা। তিনতলা বিশাল বাড়ি পাম গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে। মাঝে সুরকি ফেলা পথ। গেটের ওপরে বড় করে লেখা স্ট্রাইবারস।
বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না। এক বিশাল চেহারার মাঝবয়সি কালো মহিলা গেটের দিকে আসছেন। নিশ্চয়ই গেটে বসানো সিকিওরিটি ক্যামেরায় দেখেছেন। বেশ কড়া গলায় বলে উঠলেন, কী দরকার? কাকে চাই?
সুবীরবাবু থতমত খেয়ে বলতে শুরু করলেন।
পিকুর বাবার এয়ারক্র্যাশে মৃত্যু থেকে শুরু করে পিকুর আমেরিকায় আসা আর বাবার নাম দিয়ে সার্চ করে এখানকার অ্যাড্রেস খুঁজে পাওয়া–পুরোটাই সুবীরবাবু বললেন। যখন ওনার বলা শেষ হল, তখন ওই মহিলার চোখে জল।
মিসেস স্ট্রাইবার পিকু ও সুবীরবাবুকে নিয়ে বাড়ির দিকে চললেন। স্ট্রাইবারদের এক ছেলে। সে বাইরে একটা কলেজে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। ওনারা এ-বাড়িতে আসেন 2004-এ। ব্যাঙ্কের থেকে কেনেন। এর আগের মালিক জয়ন্ত চ্যাটার্জি ব্যাঙ্কের লোন শোধ করতে না পারায় প্রপার্টিটা ব্যাঙ্কের হাতে চলে যায়। তাই খানিকটা কম দামেই বাড়িটা স্ট্রাইবারদের কাছে চলে আসে।
সিঁড়ি দিয়ে উঠে প্রথমেই বিশাল ড্রয়িংরুম। ডান দিকে ওপরে ওঠার সিঁড়ি উঠে গেছে। তার পাশে একটা চওড়া প্যাসেজ এগিয়ে গেছে কিচেনের পাশ দিয়ে।
পিকুর দৃষ্টি লক্ষ করে মিসেস স্ট্রাইবার বলে উঠলেন,–এ বাড়ির আর্কিটেকচারটা খুব অদ্ভুত ছিল। বেসমেন্টের পুরোটা জুড়ে কোনও একটা ল্যাব ছিল। আমি যখন কিনি তখন কোনও যন্ত্রপাতি ছিল না, কিন্তু দেখেই বোঝা যায়। দশ একরের ওপর এত বড় বাড়ি। কিন্তু ঘর মোটে পাঁচটা। সবকটা ঘরই বড় বড় ছিল। আমরা ডিজাইনে বেশ কিছু চেঞ্জ করি। তা তোমার বাবা কি সায়েন্টিস্ট ছিলেন? রিসার্চ করতেন নাকি ল্যাবে?
এর উত্তর পিকুর অজানা। তবু মাথা নেড়ে সায় দিল পিকু। হঠাৎ বাইরের দিকে চোখ পড়ল পিকুর।
বাইরে কালো মেঘ জড়ো হয়েছে। লালচে আভা ছড়িয়ে পড়েছে। যে-কোনও সময়ে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হবে। অনেক রহস্য যেন লুকিয়ে আছে ওই মেঘের ঘন কালো অবয়বে। মিসেস স্ট্রাইবার জয়ন্তর সম্বন্ধে কিছুই বলতে পারলেন না। এই বাড়িতে কখনই জয়ন্তর নামে কোনও চিঠিও আসেনি। কেউ খোঁজ নিতেও আসেনি। স্ট্রাইবাররা অবশ্য ব্যাঙ্ক থেকে শুনেছিল যে জয়ন্ত প্লেন অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। আরও কিছু কথাবার্তার পর ওরা উঠতে যাবে হঠাৎ ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন,আরে ভুলেই গিয়েছিলাম। বাড়ি কেনার পর একটা ছবির অ্যালবাম ওপরের ঘরে পেয়েছিলাম। ওটা তোমাদেরই হবে। দাঁড়াও এনে দিই।
বলে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলেন। বেশ খানিক বাদে একটা অ্যালবাম হাতে নিয়ে নীচে নামলেন।
ছোট অ্যালবাম, হাতে নিল পিকু। বাবার ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় থেকে বস্টন কলোরাডো-এখানকার কিছু ছবি। এই ড্রয়িংরুমেরও ছবি আছে। মার সঙ্গে ছবি। সঙ্গে ওর। দাদাও আছে।
–আরে, এই তো তোমারও ছবি আছে। তুমিও এখানে ছিলে ছোটবেলায়!
পিকু আর বলল না যে ওটা পিকুর নয়। ঠিক ওরই মতো দেখতে ওর দাদার ছবি। এরই ছবি বাড়ির আলমারিতেও পিকু পেয়েছিল। প্রশ্নটা হল, এর কথা মা ও বাবা কেন কোনওদিন বলেনি। আর কেনই-বা এর সঙ্গে পিকুর এতটা মিল!
গাড়িতে উঠেই সুবীরবাবু প্রশ্নটা করে উঠলেন,–ওটা কি তোমার ছবি? তুমি তো এখানে আগে আসোনি? তোমার কি দাদা আছে নাকি?
–ছিল, মারা গেছেন সংক্ষেপে জানাল পিকু।
সুবীরবাবু পিকুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন,–ওহ স্যরি। কীভাবে?
পিকু চুপ করে রইল। সুবীরবাবু আর প্রশ্ন না করে গাড়ির চাবি ঘোরালেন। বলতে শুরু করলেন–আমার দাদা বছর পনেরো হল মারা গেছেন। আমি তখন এখানে।…
.
১২.
দূর থেকে মনে হয় পরিত্যক্ত বাড়ি। বাড়িতে ঢোকার রাস্তাতেও আবর্জনা পড়ে আছে। এদিক ওদিক থেকে কাটা ঝোঁপগুলো মাথাচাড়া দিয়েছে।
গ্যারেজে অনাথের মতো দাঁড়িয়ে আছে এক পুরোনো গাড়ি। নিসানের বহু পুরোনো মডেল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বেল টিপল পিকু।
–তুমি শিওর এটাই ডেভ জর্ডনের বাড়ি? সুবীরবাবু বলে উঠলেন।
–হ্যাঁ, এ অ্যাড্রেসটাই ডায়েরিতে ছিল। বাবার ডায়েরিতে।
–নাহ্, এখন আর কেউ থাকে বলে মনে হচ্ছে না। ফেরা যাক।
–আরেকটু দেখি।
আরও মিনিট দুয়েক কোনও সাড়াশব্দ নেই। ফিরতে যাবে, ঠিক সেসময় বাড়ির দরজা খুলল। মাঝবয়সি এক ভদ্রমহিলা। ভদ্রমহিলার বয়স বছর পঞ্চাশ হবে। দেখেই বোঝা যায়। একসময় খুব সুন্দর দেখতে ছিলেন। চেহারাতে শিক্ষা আর সম্রান্তির ছাপ।
–আচ্ছা এখানে কি ডেভ জর্ডন থাকতেন?
মহিলা ফ্যালফ্যাল করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর মাথা নেড়ে সায় দিলেন। আপনারা?
সুবীরবাবু হয়তো অনেক কিছু বলতে যাচ্ছিলেন; পিকু শুধু বলে উঠল, আমার বাবা হলেন জয়ন্ত চ্যাটার্জি।
–জয়ন্ত? মহিলা বিস্ফারিত চোখে পিকুর দিকে তাকালেন।
সুবীরবাবু বলতে শুরু করছিলেন,–বুঝিয়ে বলছি। জয়ন্ত চ্যাটার্জিকে আপনি চেনেন কিনা জানি না। খুব দুঃখের ঘটনা। এ ছেলেটি যখন খুব ছোট, 2002-তে ওর বাবা
ভদ্রমহিলা ডান হাত তুলে সুবীরবাবুকে থামিয়ে চারদিকে চোখ বুলিয়ে বলে উঠলেন, প্লিজ কাম ইন।
মহিলার পেছন পেছন সুবীরবাবু ও পিকু ঘরের মধ্যে ঢুকল। ঢুকেই ড্রয়িংরুম। পুরোনো কার্পেট পাতা। বেশ কিছু জায়গায় কার্পেট ছিঁড়ে কাঠের মেঝে দেখা যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে বহু পুরোনো একটা লেদার সোফাসেট।
সুবীরবাবু সোফাটা খুঁটিয়ে দেখে বসবেন কি বসবেন না ভাবছেন, এর মধ্যে ভদ্রমহিলার গলা শোনা গেল,–বসতে পারেন। ভেঙে পড়বে না।
সামনের রিক্লাইনারে হেলান দিয়ে বসে মহিলা বললেন,–আমি ডেভ জর্ডনের স্ত্রী। জুলি জর্ডন। ডেভ এয়ার ক্র্যাশে মারা যায় 2002-এ। একই ফ্লাইটে জয়ন্তও ছিল। ডেভের মৃত্যু আমার কাছে একটা বিশাল আঘাত। আজও বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পাই না। বাড়ির চেহারা দেখেই টের পেয়েছেন হয়তো। সময় এখানে গত কুড়ি বছর ধরে থেমে আছে। বলে জুলি একটু থামলেন।
জুলি ফের বলে উঠলেন,জয়ন্ত আমাদের খুব ক্লোজ বন্ধু ছিল। ও ছিল ব্রিলিয়ান্ট সায়েন্টিস্ট। কোনওদিন নোবেল প্রাইজ পেলেও অবাক হতাম না।
পিকু অবাক হয়ে বলল,আচ্ছা, বাবা তো সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন বলে আমরা জানতাম।
জুলি কষ্ট করে হেসে বললেন,–ও ওর আসল পরিচয়টা লুকোত। কেন জানি না। এমনকী বিতানও ওর কাজের ব্যাপারটা কতটা জানত জানি না। বিতানই তো তোমার মায়ের নাম, তাই না?
পিকু মাথা নেড়ে সায় দিল।
জুলি বললেন,–ওর রিসার্চের সাবজেক্ট ছিল বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং। এ বিষয়ে ও ছিল প্রথম সারির বিজ্ঞানী। ও আর ডেভ মিলে ডিএনএ সিকোয়েন্সের ওপর বেশ কিছু অসাধারণ গবেষণা করেছিল। শুধু মানুষ নয়, নানান জন্তু-জানোয়ারও ডিএনএ-এর ঠিক কী বৈশিষ্ট্যের জন্য কী স্পেশাল ক্ষমতা পায় তা নিয়েও ওদের গবেষণা অনেকদূর এগিয়েছিল। এই যেমন ধরো, কুকুরের ঘ্রাণশক্তি কিংবা গিরগিটির রং বদলানোর ক্ষমতা, বা পুমার লাফানোর ক্ষমতা–এ তো তাদের ডিএনএ-র বিশেষ সিকোয়েন্সেরই জন্য। ডেভ আর জয়ন্ত সেই সিকোয়েন্স। কী তা প্রায় জেনে গিয়েছিল। মানুষের ডিএনএ-তে কীভাবে সেই একই পরিবর্তন আনা যায় তা নিয়ে ছিল ওদের গবেষণা।
কিন্তু এসব রিসার্চ তো এখন নিষিদ্ধ। সুবীরবাবু বললেন।
–আমি তো এখনকার কথা বলছি না। তখন এসব নিষিদ্ধ ছিল না। এসব করলে কী সাংঘাতিক ফলাফল হতে পারে তার সম্বন্ধে কেউ সচেতন ছিল না।
–তা এসব করে লাভ কী হত? সুবীরবাবু ফের প্রশ্ন করলেন।
কী আবার! মানুষ যদি ঈগলের মতো দূর থেকে দেখতে পেত বা আঙুল কেটে গেলে নিজের থেকে তৈরি করতে পারত তাহলে নিশ্চয়ই ভালো হত, তাই না? কেউ যদি চিতাবাঘের মতো দৌড়োতে পারত আর সিংহের মতো শক্তিশালী হত তাহলে তাকে কি আর সাধারণ মানুষ প্রতিযোগিতায় হারাতে পারত? হয়তো ওরা অতিমানব তৈরি করার চেষ্টা করছিল।
–কিন্তু আমার বাবাই কখনই এরকম কিছু করতে পারে না। বাবাইকে যতটুকু দেখেছি, বাবাই সম্বন্ধে যা শুনেছি বাবাই কখনও অন্যায় কিছু করত না। এভাবে অতিমানব তৈরি করা এতো একধরনের অন্যায়। সাধারণ মানুষ কি টিকে থাকতে পারবে এদের সঙ্গে লড়াই করে?
হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ। জয়ন্ত নিজের ইচ্ছেতে এরকম কিছু করত না। ও মানুষ হিসেবেও ছিল খুব বড়। দার্শনিকের মতো কথা বলত মাঝেমধ্যে। খুব দূরদৃষ্টি ছিল। আমার মনে হয় না ওরা এই ভুল করত। কিন্তু আমার কেন জানি না মনে হত ওরা খুব ভয়ে ভয়ে ছিল শেষের কয়েকটা বছর। কেউ যেন আড়াল থেকে ওদের কন্ট্রোল করত। ডেভ আমার সঙ্গে কোনও কথা বলত না। কথায় কথায় অন্যমনস্ক হয়ে যেত। কলিংবেল-এর আওয়াজে নার্ভাস হয়ে পড়ত। অচেনা নাম্বার থেকে ফোন এলে ধরত না।
–এটা কোন সালের কথা?
–এই ধরো, 2000 থেকে 2002–এই দু-বছর। তখন ওকে আমি দেখেছি সম্পূর্ণ। অন্যরকম হয়ে যেতে।
–আমার বাবা তো ওই সময় ভারতে চলে যান।
–হ্যাঁ, কিন্তু ও এখানে প্রায়ই আসত। ওরা দুজনে মিলে ওপরের ঘরে বসে অনেক রাত অবধি কীসব আলোচনা-গবেষণায় ব্যস্ত থাকত। এখানে তোমাদের একটা বাড়িও ছিল, তা জানো তো? সেখানেও ডেভ আর জয়ন্ত অনেক সময় একসঙ্গে কাটাত। তারপর একদিন হঠাৎ সব শেষ হয়ে গেল। এয়ার ক্র্যাশে।
জুলি থামলেন। ঘরে পিনড্রপ সাইলেন্স। খানিকবাদে পিকুই নীরবতা ভঙ্গ করল।
–আপনি গিয়েছিলেন ক্র্যাশ সাইটে?
–হ্যাঁ, কিন্তু ওখানে তো ওরা একেবারে কাছে যেতে দেয়নি। বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে প্লেনের ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে পড়েছিল। পুরো জায়গাটা ঘিরে রেখেছিল ওরা।
–ডেডবডি দেখেছিলেন?
সবাই এত পুড়ে গিয়েছিল যে কাউকে চেনার উপায় ছিল না। তবে ক্রেডিট কার্ড, আইডি–এসব থেকে ক্র্যাশ ইনভেস্টিগেশন টিম ওদের সনাক্ত করে। তবে ওরা যে মারা গিয়েছিল তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।
–আপনার কি সত্যিই কোনও সন্দেহ নেই এ ব্যাপারে? পিকু বলে উঠল। ওর কেন জানি না মনে হল ভদ্রমহিলা নিজেই নিজেকে বোঝানোর চেষ্টা করছেন। তা না হলে হঠাৎ ওকথা বললেন কেন?
খানিকক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে পিকুর দিকে তাকিয়ে রইলেন জুলি। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,কফি চলবে? কফি খেতে খেতে বলব।
ঘরের পরিবেশ বেশ ভারী হয়ে আছে। সেই ভার খানিকটা কাটাতেই পিকু সায় দিল।
খানিকবাদে কফি, কিছু স্ন্যাকস আর সসেজ নিয়ে ফিরে এলেন জুলি। পিকুর কেন জানি না মনে হল বহু বছর বাদে জুলি যেন কথা বলার লোক খুঁজে পেয়েছেন। যে সব কথা কাউকে কোনওদিন বলা যায়নি, সেসব যেন বলার সময় এসেছে।
কফিতে চুমুক দিয়ে জুলি বলে উঠলেন,আচ্ছা কেউ কি এরকম অ্যাক্সিডেন্টে মারা যাওয়ার আগে মৃত্যু টের পায়? আমার কেন জানি মনে হয় ডেভ বুঝতে পেরেছিল যে আমাকে চিরকালের মতো ছেড়ে চলে যাবে। তাই ওর সব ভালোবাসা-দরকারি সব কথা ও যেন জানিয়ে গিয়েছিল শেষের কদিনে। দরকারি সব কম্পিউটারের ফাইল নিউইয়র্কে যাওয়ার কয়েকদিন আগে দেখিয়ে দিয়েছিল। আমি তখন খানিকটা অবাকই হয়েছিলাম।
নিউইয়র্ক?
–হ্যাঁ, ও শেষ এক সপ্তাহ নিউইয়র্কে ছিল। একটা মেডিক্যাল কনফারেন্সে। সেখান থেকে ফিরতে গিয়েই এই এয়ারক্র্যাশ হয়। তোমারও কি তোমার বাবার সম্বন্ধে একথা মনে হয়েছিল?
পিকুকে চুপ থাকতে দেখে জুলি ফের বলে উঠলেন,–অবশ্য তুমি আর কী বুঝবে? তুমি তো তখন অনেক ছোট।
পিকু একটু চুপ থেকে বলল,ছোটবেলায় কিছু বুঝতে না পারলেও সম্প্রতি আমারও একই কথা মনে হয়েছিল, আর তাই আমি এখানে–
বলে ও ছোটবেলার লুডোর কথাটা খুলে বলল।
মন দিয়ে শুনে জুলি বললেন,–এই এয়ারক্র্যাশটার ব্যাপারে যে চিফ ইনভেস্টিগেটর ছিল তার সঙ্গে আমি দেখা করি। প্রথমে কিছু বলতে চায়নি। কিন্তু আমি কয়েকমাস ধরে লেগে থাকি। জানতে পারি ওনার বেশ কিছু সন্দেহ হয়েছিল। ওনারও মনে হয়েছিল ফ্লাইটে কোনও ধরনের বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে। অজানা কারণে ব্ল্যাকবক্সে কিছুই ধরা পড়েনি। টেররিস্ট অ্যাকটিভিটি-ও হতে পারে। কিন্তু ওনাকে সেটা প্রকাশ করতে দেওয়া হয়নি। তা ছাড়া উনি দেখেছিলেন সেদিনকার ওই ফ্লাইটে ফাইনালি কারা উঠেছিল সেই নামের লিস্টও নেই। ওনার মনে হয়েছিল যে কেউ যেন ওই ডেটা এয়ারলাইনস-এর ডেটাবেস থেকে ইচ্ছে করেই উড়িয়ে দিয়েছে যাতে কেউ না জানতে পারে প্লেনে কে কে ছিল।
আশ্চর্য! কিন্তু আপনি এটা জানার পর কিছু করেননি?
–চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কোনও ফল হয়নি। ইনভেস্টিগেশন জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।
কফির কাপটা টেবিলের ওপর রেখে জুলি যেন প্রসঙ্গ বদলানোর জন্যই বললেন, তা, তোমার নাম কী?
–পিকু।
বাহ, সুইট নেম। তোমার বাবার কথা নিশ্চয়ই খুব মনে পড়ে।
মাথা নেড়ে সায় দিয়ে পিকু বলে,–আচ্ছা আমার দাদাকে কি আপনি দেখেছিলেন?
–হ্যাঁ, তোমার দাদা এখানেই মারা যায়, চার কি পাঁচ বছর বয়সে। তখন তোমার বাবা-মা কলোরাডোতে। খুব সম্ভবত 1996-এ। হঠাৎ দুদিনের এক অজানা জ্বরে তোমার দাদা মারা যায়। ভারি মিষ্টি ছিল ছেলেটা। তোমার বাবা-মা খুব ভেঙে পড়েছিল। প্রথম সন্তান বলে কথা! তোমার বাবা ওর ডিএনএ পর্যন্ত সংগ্রহ করে রেখে দিয়েছিল। তুমি বাড়িতে ওর কোনও ছবি দ্যাখোনি?
না, আগে দেখিনি। কিছুদিন আগে ইন্ডিয়াতে একটা আলমারির ভেতর থেকে প্রথম ওর একটা ছবি পাই। প্রথমে ভেবেছিলাম আমারই ছোটবেলার ছবি। পরে খুঁটিয়ে দেখে বুঝি যে ওটা আমার নয়, কিন্তু অবিকল আমারই মতো দেখতে।
–তোমারই মতো? দ্যাট মিনস–বলে চুপ করে গেলেন জুলি।
কী?
দ্যাট মিনস–তুমি হোচ্ছ তোমার দাদার ক্লোন। তোমাদের দুজনেরই একই ডিএনএ। তাই একরকম দেখতে। তোমার দাদার ডিএনএ তো ছিলই। তা থেকে ক্লোনিং টেকনোলোজি ব্যবহার করে সেই ভ্রুণ থেকে তোমাকে তৈরি করা হয়। ক্লোনিং কী করে করতে হয় তা জয়ন্ত তার মানে জেনে গিয়েছিল।
–1997-এ ক্লোনিং! হেসে উঠলেন সুবীরবাবু।
–অন্য কেউ হলে আমিও বিশ্বাস করতাম না। এখনই যেটা সম্ভব হয়নি তা পঁচিশ বছর আগে! জুলি একটু থেমে ফের বলেন, জয়ন্ত ওর সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে ছিল। বুদ্ধির দিক থেকে ও নিজেই ছিল অতিমানব। ওর পক্ষে কিছুই অসম্ভব ছিল না। তা ছাড়া এখনও আমার মনে পড়ে ও আর বিতান তোমার দাদা মারা যাওয়ার পর কীরকম ভেঙে পড়েছিল। তার কিছুদিন পরের কথা, আমরা জানতে পারি যে জয়ন্ত তোমার দাদার ডিএনএ সংগ্রহের ব্যবস্থা করেছে। তখন আমি জিগ্যেস করতে তোমার বাবা বলেছিলেন, আমি শান্তনুকেই ফিরে পেতে চাই। ছেলে হলে ওরকমই ঠিক হতে হবে। আমি ওকে ফিরিয়ে আনবই। কথাটার মধ্যে এমন একটা একগুয়েমি ছিল যে আমি খুব অবাক হয়ে যাই।
–আমারও ছোটবেলাতে কেন জানি মনে হত আমার সঙ্গে অদৃশ্য কারুর যেন তুলনা চলছে। আমি যেন ঠিক তারমতো হলে বাবা-মা খুব খুশি হন। বলতে বলতে থেমে গেল পিকু।
যেখানে পিকু বসেছে তার সামনেই ইউরোপিয়ান ভিক্টোরিয়ান স্টাইলের বড় জানলা। খানিকটা দূরে একটা ওক গাছ। ও দিকটা পুরো জঙ্গল হয়ে আছে। কেন জানে না ওর মনে। হল গাছের ঝোপের মধ্যে কেউ একটা দাঁড়িয়ে ছিল। এদিকে লক্ষ করছিল। দ্রুত অন্য একটা ঝোপের পেছনে চলে গেল। মনে হল লোকটার গায়ের রং যেন সবুজ। আর তাই আগে চোখে পড়েনি। জানলার কাছে গিয়েও চোখে কিছু পড়ল না।
কথাটা আর বলল না পিকু, কিন্তু আলোচনার সুর যেন কেটে গেল। আরও আধঘণ্টা পরে ওরা জুলির কাছ থেকে বিদায় নিল। জুলি গাড়ি অবধি এগিয়ে দিতে এসে বলে উঠলেন, আবার এসো। অনেকদিন বাদে মনে হল আমি যেন সেই দিনগুলোতে ফিরে যেতে পেরেছি। আমার নাম্বারটা রেখেছ তো? কোনও দরকারে ফোন কোরো। আমি ডেভ-এর পুরোনো ডায়েরি, অ্যালবাম ঘেঁটে দেখব যদি ওখান থেকে কোনও সূত্র মেলে। এর পেছনে বড় কোনও শক্তি, বড় কোনও রহস্য আছে। আমার মনে হয় ডেভ আর জয়ন্ত দুজনকেই মার্ডার করা হয়েছে। ওরা হয়তো সেটা আগে থেকেই টের পেয়েছিল। প্রশ্নটা এখানেই যে কেন ওদের মারা হল, আর সব জেনেও ওরা চুপ করে বসে রইল কেন? বিপক্ষশক্তি কি সত্যিই এতটাই শক্তিশালী ছিল যে ওদের কোনও বাঁচার উপায়ই ছিল না? আমার এক বন্ধু ইউ এস সেক্রেটারি অফ ডিফেন্সকে ভালো করে চেনে। আমি তার সঙ্গে আবার কথা বলব, যাতে তদন্ত আবার চালু করা হয়।
গাড়িতে উঠে বসল ওরা। সুবীরবাবু হঠাৎ করে 40 স্পিড লিমিটের রাস্তায় 100 তুলে বলে উঠলেন,বুঝলে পিকু, সারা জীবনটা বড্ড একঘেয়ে ভাবে কাটালাম। রোজই এক রুটিন। রোজই নিয়ম মেনে সব কিছু করা। না আছে কোনও চমক, না আছে কোনও অ্যাডভেঞ্চার। আজ কেন জানি মনে হচ্ছে বড় একটা রহস্যের মধ্যে ঢুকে গেছি।
ওনার জেমস বন্ড স্টাইলের ড্রাইভিং অবশ্য বেশিক্ষণ চলেনি। পেছনে লাল-নীল আলো জ্বেলে একটা পুলিশের গাড়ি তাড়া করেছে। পরের আধঘণ্টা ঠিক রুটিনমাফিক হয়নি।
.
১৩.
রবার্ট ওর কম্পিউটারে অফিসের পুরোনো ফাইলগুলো দেখছিল। সিআইএ-র ডিরেক্টর হিসেবে ওর হাতে বেশ কিছু পুরোনো প্রোজেক্টের ইনফরমেশন এসেছে। বেশিরভাগই খুব সেনসিটিভ ডেটা। প্রত্যেকটা ফাইল খোলার আগে ডানহাতের পাঁচটা আঙুলের ফিঙ্গারপ্রিন্ট আর রেটিনা স্ক্যান করার দরকার হচ্ছে। তা ছাড়া নানান ধরনের পাসওয়ার্ড তো আছেই।
প্রসেসটা খুব স্লো। কিন্তু উপায় নেই। সাবধানতার কোনও বিকল্প নেই। প্রত্যেকটা প্রোজেক্টের ইনফরমেশন ওর জানা দরকার। অন্যান্য অফিসের মতো আগের বিদায়ী ডিরেক্টর কোন প্রজেক্টের কী স্ট্যাটাস তা বুঝিয়ে হ্যান্ডওভার করবে–তা তো আর CIA-তে হয় না! ইনফ্যাক্ট আগের জন কে ছিলেন, তাও জানে না রবার্ট। এতটাই গোপনীয়তার সঙ্গে এখন পুরো তথ্য লুকিয়ে রাখা হয়। এখানে যার যতটুকু জানা দরকার, তার থেকে একটুও বেশি কেউ জানবে না।
গত এক সপ্তাহে বাকি সব প্রোজেক্টের লেটেস্ট স্ট্যাটাস জেনে নিয়েছে রবার্ট–শুধু একটা বাদে। প্রোজেক্ট এইচ। ফাইলটা ব্ল্যাঙ্ক। ওই একটা অক্ষরের বাইরে কোথাও কোনও ইনফরমেশন নেই। অথচ গুরুত্বপূর্ণ প্রোজেক্টের লিস্টে প্রোজেক্ট এইচ নামটা দিব্যি জ্বলজ্বল করছে।
একটা বিশেষ নাম্বারে ডায়াল করলেন রবার্ট। বিশেষভাবে সুরক্ষিত হেল্পডেস্ক। একটা স্পেশাল কোড আর বায়োমেট্রিক স্ক্যানের পরে প্রোজেক্ট এইচ-এর তথ্য জানানোর জন্য অনুরোধ করলেন রবার্ট। উলটোদিক থেকে যান্ত্রিক গলায় একটা কোড শোনা গেল। বিশাল বারো ডিজিটের কোডটা শোনার পর অবাক হয়ে বসে রইলেন রবার্ট। কোড থেকে একটা জিনিসই জানা যাচ্ছে যে প্রোজেক্ট এইচ খুবই গোপনীয় কোনও প্রোজেক্ট। এই প্রোজেক্টের ইনফরমেশন পেতে রীতিমতো কাঠখড় পোড়াতে হবে।
ফোনে রিং হচ্ছে। ফোনটা ধরলেন রবার্ট।
–হ্যালো।
–কোডটা জানান। যান্ত্রিক গলা বলল।
ফোনের কি প্যাডে কোডটা ডায়াল করলেন রবার্ট। খানিক আগেই পাওয়া প্রোজেক্ট এইচ-এর কোডটা। আরও নানান ধরনের ভেরিফিকেশনের পর উলটোদিক থেকে শোনা গেল– প্রোজেক্ট এইচ হচ্ছে সিআইএ ও ডিফেন্স অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রোজেক্ট এজেন্সির (DARPA) যুগ্ম উদ্যোগে একটা বিশেষ প্রোজেক্ট। মূল উদ্দেশ্য যুদ্ধের জন্য স্পেশাল আর্মি তৈরি করা, যারা বুদ্ধিতে, শক্তিতে, গতিতে সাধারণ সৈন্যদের থেকে অনেক এগিয়ে থাকবে।
উদ্দেশ্য?
–যাতে আমেরিকা যে-কোনও বিদেশি শক্তির বা টেররিস্ট আক্রমণের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে। আর পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী দেশ হিসেবে নিজের অবস্থান বজায় রাখতে পারে। শুধু তাই নয়, কখনও যদি মানুষের অস্তিত্ব রোবট বা যান্ত্রিক শক্তির কাছে বিপন্ন হয়ে পড়ে তাহলে এরাই হবে ভরসা।
–এ প্রোজেক্ট কি আমারই আন্ডারে পড়বে?
–অবশ্যই, তা না হলে এতটা ইনফরমেশন আপনাকে দেওয়া হত না।
–তা প্রোজেক্টের বর্তমান অবস্থা কী?
–শেষের দিকে। শেষ পর্যায়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।
–কোথায় হচ্ছে প্রোজেক্টটা?
–জানানো যাবে না।
–কিন্তু আমি না জানলে চলবে কী করে?
দরকার মতো প্রোজেক্টের স্ট্যাটাস আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হবে। কোনওভাবে কাউকে এ প্রোজেক্ট সম্বন্ধে জানানো যাবে না।
–এ প্রোজেক্ট কবে শুরু হয়েছিল? কার আন্ডারে আছে?
–2001-এর 11 সেপ্টেম্বরের পরে এ প্রোজেক্ট শুরু হয়। তিনজন DARPA-র বিজ্ঞানী আর দুজন সিনিয়ার মিলিটারি অফিসার নিয়ে এর কোর টিম। তারাই এ প্রোজেক্ট পরিচালনা করে।
তাদের পরিচয় জানা যাবে?
না।
–প্রেসিডেন্ট কি এ প্রোজেক্টের ব্যাপারে জানেন?
–খুব সামান্য। আপনি ঠিক যতটা জানলেন। ওই কোর টিমের বাইরে কেউ এই প্রোজেক্ট সম্বন্ধে জানে না।
–আপনার নাম? আপনিও কি এ প্রোজেক্টের সঙ্গে যুক্ত আছেন?
উলটোদিকের ফোন কেটে গেল।
–ননসেন্স! বলে রবার্ট উঠে দাঁড়ালেন। দায়িত্বও নিতে হবে, আবার কোনও কিছু জানাও যাবে না। কোনও মানে হয়? সেক্রেটারিকে পলকে ঘরে ডেকে নিলেন রবার্ট।
–পল, প্রোজেক্ট এইচ-এর যাবতীয় ইনফরমেশন আমার চাই। গত একসপ্তাহ ধরে আমার যত সোর্স ছিল আমি ভালো করে দেখেছি–তেমন কোনও তথ্য নেই। তুমি তো অভিজ্ঞ লোক। আশাকরি বলতে হবে না, কী করে এর সম্বন্ধে ডিটেলস বার করতে হয়। দরকার হলে আমাদের দেশের বেস্ট কম্পিউটার হ্যাঁকারদের নিয়োগ করো। আই মাস্ট হ্যাভ দিস ইনফরমেশন।
–ঠিক আছে। রবার্টের স্থির দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে পল বিষয়টার গুরুত্ব বুঝতে পারল। আর কোনও প্রশ্ন না করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।
.
১৪.
রাত বারোটা। লাসভেগাস। শহর যেন সবে ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে। আলোর রোশনাই মুখ থুবড়ে পড়েছে চওড়া চওড়া রাস্তায়। ঝকমকে আলো, হাজারো পথচারী, লাসভেগাস বুলেভার্ডের। ধারে আলোয় ভাসা ফোয়ারা সবমিলিয়ে চারদিকে উৎসবের আবহ। এখানে কেউ কোন দিকে যাচ্ছে তা জেনে হাঁটে নাকী দেখতে যাচ্ছে ভেবে এগিয়ে যায় না। পুরো শহরটাই ঘুরে দেখার। আনন্দের উত্তাপই এখানে বড় প্রাপ্তি। চারদিকে আকাশচুম্বী হোটেল আর ক্যাসিনো। নানান ধরনের শো হচ্ছে। সাধারণ লোকের সঙ্গেই মিশে আছে পুলিশের লোক। রোবট পুলিশ কন্ট্রোল করছে হামাগুড়ি দিয়ে এগোনো ট্রাফিককে। এখানে প্রতি মুহূর্তে কোটি টাকা হাত বদলাচ্ছে ক্যাসিনোর মধ্যে।
এরকমই একটা ক্যাসিনোর নাম হল লা রোমা। ঝাঁ-চকচকে হোটেলের পুরো নীচের ফ্লোরে প্রায় এক বর্গমাইল জুড়ে বিশাল ক্যাসিনো। ক্যাসিনোর ভেতরে প্রচুর সিকিউরিটি জায়গায় জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। তাদের প্রত্যেকের হাতে অত্যাধুনিক বন্দুক। দরকার হলে গুলি চালাতে দ্বিধা করবে না।
জন এ হোটেলের সিকিউরিটি হেড হিসেবে প্রায় দশ বছর কাটিয়ে দিয়েছে। অন্য বেশিরভাগ রাতের মতো আজকের রাতও ঘটনাহীন। পেশাদারি গ্যাম্বলারদের ভিড় বেশিরভাগ খেলায়। এরা কোটি কোটি টাকা বাজি ধরে খেলে। লক্ষ টাকা হারলেও এরা উত্তেজিত হয়ে ওঠে না। কিছু নতুন অচেনা মুখ কৌতূহলী হয়ে মাঝেমধ্যে খেলছে।
সেরকমই একটা নতুন মুখকে বেশ খানিকক্ষণ ধরে দেখছে জন। ভারি সুন্দর দেখতে। ফরসা মাঝারি হাইট। তীক্ষ্ম বুদ্ধিদীপ্ত নীল চোখ। মাথা ভরতি কঁকড়া চুল। হাঁটাচলা দেখলেই বোঝা যায় সে ক্যাসিনোতে কখনও আসেনি। সবরকম খেলা ঘুরে ঘুরে দেখছে। নিয়ম বোঝার চেষ্টা করছে। টেবিলের শুটারদের মাঝেমধ্যে জিজ্ঞাসা করছে। এখানে এরকম অনেকেই আসে। কিন্তু জনের অভিজ্ঞ চোখ তাদের সবাইকে অনুসরণ করে না।
তার কারণ ছেলেটা খেলছে, আর নতুন হলেও বেশিরভাগই জিতছে। আর বেটও করছে। বড় বড় টাকার অঙ্ক–যা বড় জুয়াড়ি ছাড়া কেউ করে না।
জন শুধু সিকিউরিটি হেড নয়, বিজ্ঞানের ভালো ছাত্র। এই খেলাগুলোর পেছনে ভাগ্য ছাড়াও বুদ্ধি কাজ করে। তার থেকেও বড় কথা যে এরকম বারবার জিতছে, সে কোনও চুরি করছে না তো? প্রযুক্তি এখন এতটাই এগিয়ে গেছে যে কে কীভাবে তাকে প্রয়োগ করে তাও বোঝা মুশকিল। এই তো মাসখানেক আগে একজন এখানে রেটিনাতে মিনি ভিডিয়ো রেকর্ডার। ইমপ্ল্যান্ট করে এসেছিল।
ছেলেটা এক বোর্ডে বেশিক্ষণ খেলছে না। দু-তিনবার জেতার পরে অন্য বোর্ডে চলে যাচ্ছে। বোর্ডের চারদিকে লুকিয়ে রাখা আছে মাইক্রো-ভিডিয়ো ক্যামেরা। যে-কোনও জাল কারচুপি ওতে ধরা পড়ে যায়। তাতেও খুঁটিয়ে বেশ খানিকক্ষণ দেখল জন। নাহ্, ছেলেটার কাছে তো সেরকম কোনও যন্ত্র নেই!
ছেলেটা এবার স্কিল জোনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আগের ক্যাসিনোর গেমগুলোতে ভাগ্যই একটা বড় ফ্যাক্টর ছিল। যতই বুদ্ধি থাকুক না কেন, ভাগ্য সঙ্গে না থাকলে জেতা শক্ত। কিন্তু স্কিলজোন অন্যরকম। এই গেমে লাকের থেকে আগে থাকে স্কিল, ইনটেলিজেন্স।
ছেলেটা ওখানে গিয়েও একের পর এক জিততে শুরু করল। কালার রেস। একটা গোলাকার জায়গার নানা অংশে বারবার নানান রং ফুটে উঠছে খুব দ্রুত। দু-মিনিটের মধ্যে কোন রং কতবার হয়েছে সেটা বলতে হবে।
যে ঠিক সংখ্যার সব থেকে কাছাকাছি বলবে সে জিতবে। ছেলেটা এটাও তিনবার জিতল। তারপর প্রায় বিরক্ত হয়েই পাশের গেমটার দিকে এগিয়ে গেল। নাম্বার সিকোয়েন্স গেম। একটার পর একটা সংখ্যা ফুটে উঠেছে, আর তার মধ্যে আছে দুর্বোধ্য প্যাটার্ন। মাঝে মাঝে ওই সিকোয়েন্সের পরের সংখ্যাটা অনুমান করতে হচ্ছে। সময় খুব কম। তারমধ্যে যে আগে ঠিক বলতে পারবে সেই জিতবে।
জন জানে যে এসব গেমে যারা যোগ দেয় তারা প্রত্যেকেই এ বিষয়ে এক্সপার্ট। মাসের পর মাস-বছরের পর বছর প্র্যাকটিসের পরে এখানে আসে। বিশেষ করে এসব ক্যাসিনোতে এসে যারা বেটিং করে তারা সবরকম সাবধানতা নিয়েই নামে। কিন্তু এ ছেলেটা এসে যেন আজকে সবার প্ল্যান ভণ্ডুল করে দিয়েছে। এটাও হেসেখেলে দুবার জিতে নিল। তারপর আরেকটা বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল।
এবার জন এগিয়ে এল। আর আড়াল থেকে দেখার দরকার নেই। নিশ্চিত কিছু গন্ডগোল আছে। জনকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে ও এখানকার সিকিউরিটিতে আছে। সাধারণ পোশাক।
জন ছেলেটার কাছে গিয়ে বলে উঠল, বাহ, তুমি তো দেখলাম অসাধারণ প্লেয়ার। একের পর এক জিতছ। তোমার নাম কী?
–পল। একঝলক জনের চোখের দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল ছেলেটা। তারপর অন্য কোনও বোর্ডের দিকে না তাকিয়ে ক্যাসিনোর ফ্লোর থেকে বেরোতে গেল।
জন দ্রুত পায়ে পিছু নিয়ে ফের বলে উঠল, তুমি কোথা থেকে এসেছ?
ক্যালিফোর্নিয়া।
আমি এখানকার সিকিউরিটি। তোমার আইডিটা দেখি।
ছেলেটা কোনও দ্বিধা না করে ওয়ালেট থেকে ড্রাইভিং লাইসেন্স বার করে তুলে ধরল। জন একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল। নাহ, আইডিতে কোনও গন্ডগোল নেই। ক্যালিফোর্নিয়া স্টেটের লাইসেন্স। ছেলেটার বয়স মোটে কুড়ি। তবু একে এত সহজে ছাড়া যাবে না। জানা দরকার কীভাবে সমানে জিতে চলেছে।
–তুমি আমার সঙ্গে একবার আমাদের সিকিউরিটি রুমে চলো। দরকার আছে।
জন ভেবেছিল যে ছেলেটাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য ভয় দেখাতে হবে। বলপ্রয়োগেরও দরকার হতে পারে। তাই এক বিশালদেহী গার্ডকে ইতিমধ্যেই ডেকে নিয়েছিল। কিন্তু তার কোনও দরকার হল না। ছেলেটা বেশ হাসিমুখেই ওর পিছু পিছু এগিয়ে চলল।
বিশালদেহী কালো গার্ডটা ছেলেটার পাশে পাশে হাঁটছিল। এসক্যালেটরের পাশ দিয়ে যাচ্ছে, হঠাৎ পেছনে একটা আওয়াজ হল। জন মাথা ঘুরিয়ে দেখল যে গার্ডটা মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে।
জন দেখতে না পেলেও আরেকটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা আরেকজন গার্ডের চোখ এড়ায়নি ঘটনাটা। সে আঙুল তুলে ছেলেটার দিকে ছুটে এল।
–ও ঘুষি মেরে জোকোকে ফেলে দিয়েছে।
বলে রিভলভারটা ছেলেটার দিকে তুলে ধরল। তুলে ধরার চেষ্টা করল বলাই ভালো। কারণ, তার আগেই ছেলেটা বিদ্যুৎবেগে এগিয়ে গিয়ে রিভলভারটা কেড়ে নিয়ে ওর হাত ধরে এমনভাবে হ্যাঁচকা টান দিল যে গার্ডটা পাঁচ হাত দূরে ছিটকে পড়ল। আর কেউ এগিয়ে আসার আগেই তিন-চার লাফে কুড়ি ধাপের সিঁড়ি টপকে বেরিয়ে গেল। ক্যাসিনো থেকে বেরোনোর দরজা বেশ খানিকটা দূরে। কিন্তু খানিকটা ছুটে গিয়েও জন বা কোনও সিকিউরিটি গার্ড ছেলেটার টিকিও আর দেখতে পেল না। কর্পূরের মতো হাওয়ায় উবে গেছে যেন।
.
১৫.
সুবীরবাবু মিসিগান ইউনিভার্সিটি দেখাতে নিয়ে এসেছিলেন পিকুকে। বহু পুরোনো ইউনিভার্সিটি। চারটে জায়গায় ছড়ানো ক্যাম্পাস। নর্থ সাউথ, সেন্ট্রাল আর মেডিক্যাল। পুরোনো বিল্ডিংগুলোর। পাশাপাশি নতুন বিল্ডিং হয়েছে একই ধাঁচের। এমনভাবে তৈরি করেছে যে কোনটা পুরোনো আর কোনটা নতুন ভেতরে না ঢুকলে বোঝার উপায় নেই। ওখানে প্রায় একঘণ্টা কাটিয়ে ইউনিভার্সিটির আশেপাশের এলাকা দেখাতে শুরু করলেন সুবীরবাবু।
ইউনিভার্সিটি ছেড়ে খানিকটা এগোতে হঠাৎ পিকু দেখল পাশের একটা সরু রাস্তা ব্লক করে রাস্তাতে চেয়ার টেবিল পেতে চেস খেলা হচ্ছে। এরকম দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না, গাড়ি পার্ক করে ওরা দুজনেই নেমে এল।
ওপেন চেস টুর্নামেন্ট। যে কেউ খেলতে পারে। সবে শুরু হয়েছে, চলবে রাত অবধি। পুরস্কার মূল্য পাঁচ হাজার ডলার। একটা লোকাল কোম্পানি স্পনসর করছে।
–কি, খেলবে নাকি? সুবীরবাবু জিগ্যেস করলেন।
হ্যাঁ, খেললে খারাপ হয় না। আমি খারাপ খেলি না।
–তা খেলো না! আমিও বসে বসে দেখি। বেশ ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে। ওই তো দর্শকদের বসার জায়গাও আছে।
দাবাটা চিরকালই পিকুর প্রিয় খেলা। বাবাও নাকি খুব ভালো দাবা খেলত। পিকু স্কুলে বরাবর চ্যাম্পিয়ন হয়ে এসেছে। তবে বড় টুর্নামেন্ট কখনও খেলেনি। খানিকক্ষণের মধ্যে পিকুও যোগ দিল। আর জিততেও শুরু করল। স্পিড চেস। একেকটা ম্যাচ দশমিনিটের।
বেশিরভাগই সাধারণ মানের প্লেয়ার। চারটে রাউন্ডের পরে সেমিফাইনাল। সেমিফাইনালে উঠে একটা ছেলের কাছে পিকু হেরে গেল। সেই ছেলেটাই পরে টুর্নামেন্টটা জিতল। অসাধারণ খেলে। চাল দিতে এক সেকেন্ডও টাইম নেয় না। সেরকমই বুদ্ধির ছাপ চালে। পিকু ভেবে রেখেছিল টুর্নামেন্টের পরে ছেলেটার সঙ্গে আলাপ করবে। কিন্তু হঠাৎ ওর চোখ পড়ল সুবীরবাবুর দিকে। খানিকদূরে একজন মোটা গোলগাল চেহারার সাহেবের সঙ্গে পাশাপাশি চেয়ারে বসে আছেন। সাহেবের চোখ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে আর সেই অশ্রুসজল চোখে সাহেব পিকুর দিকেই তাকিয়ে আছে। আন্দাজ করতে দেরি হল না কী হয়েছে। সুবীরবাবু হাত নেড়ে পিকুকে ডাকলেন।
–এনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি মিসিগান ল স্কুলের লাইব্রেরিয়ান। সাইমন। তোমার কথাই হচ্ছিল।
সাইমন কোনও কথা না বলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন পিকুকে।
–ঈশ্বর তোমার সঙ্গে থাকুন। বাবার খোঁজে দশ বছর ধরে তুমি দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ। আর আমি কীরকম অভাগা দেখ! আমার ছেলে একই শহরে থাকে–অথচ খোঁজই নেয় না।
ভদ্রলোকের কান্না একটু কমলে পাশ থেকে সুবীরবাবু বলে উঠলেন,–যে ছেলেটা জিতল তার নাম ড্যানিয়েল। ও পড়াশোনাতেও নাকি খুব ভালো। ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়ছে। প্রথম হয়। ওর সঙ্গে যাকে সবসময় দেখা যায়,–ওর সেই বন্ধু আজকে আসেনি। সে আবার সম্প্রতি নাকি এখানকার একটা রেসে একশো মিটারে ওয়ার্ল্ড রেকর্ড ভেঙেছে। তা নিয়ে এখনও অনেক কাগজে লেখালেখি চলছে। সে-ও পড়াশোনায় খুব ভালো।
সাহেব বসে চোখমুখ রুমালে মুছতে মুছতে বলে উঠলেন,–ওরা দুজনেই একটা অরফানেজে বড় হয়েছে। তোমারই মতো। দুজনেই অসম্ভব ট্যালেন্টেড। অলরেডি বেশ কিছু পাথব্রেকিং রিসার্চও করছে। তা তুমিও তো খুব ভালো খেলছিলে। ওই ছেলেটা না থাকলে তুমিই জিততে।
একটু থেমে সাইমন সুবীরবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি ইউনিভার্সিটির সব ইনফরমেশন ঘেঁটে দেখব। যদি পিকুর বাবার কোনও খোঁজ পাই, জানাব। আজ উঠি। ওকে দেখলেই…। বলে আবার কেঁদে ফেললেন, আরেকবার পিকুকে জড়িয়ে ধরে বিদায় নিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠলেন।
পিকু সুবীরবাবুর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল,আপনি কী কী বলেছেন বলুন তো? দশ বছর ধরে দেশ-বিদেশে খুঁজছি! সারা শহরকে কাঁদিয়ে বেড়াচ্ছেন।
–আহা, ওই হল। উনিশ-বিশ। চলো গাড়িতে ওঠা যাক। সারাদিন আজ বেশ কাটল। সাইমন লোকটাও বেশ ভালো।
গাড়ির দিকে দুজনে এগোতে যাবে, দেখতে পেল টুর্নামেন্টে জেতা ছেলেটা পাশেই ওর গাড়িতে উঠতে যাচ্ছে। পিকুকে দেখে এগিয়ে এল। হ্যান্ডশেক করে বলে উঠল–আমি ড্যানিয়েল।
–তুমি খুব ভালো খেলছিলে। আমি না থাকলে তুমিই জিততে। তুমি কি এখানেই থাকো?
না, আমি এখানে একটা রিসার্চের কাজে এসেছি। তুমি তো শুনলাম ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর স্টুডেন্ট। খুব ভালো রিসার্চ করছ।
–হ্যাঁ, ওই আর কী! দাবাটা হল আমার প্রাণ। তা, তোমার সঙ্গে যে জন্য কথা বলতে এলাম,–আমি যেখানে বড় হয়েছি, সেখানে একজনকে চিনতাম যাকে দেখতে ঠিক তোমার মতো। খুব আশ্চর্য মিল।
তুমি বড় হয়েছ কোথায়?
ক্যালিফোর্নিয়ায়। ওখানে এক অরফানেজে। যার কথা বলছি সে আমাদের থেকে কয়েকবছর বড়। এক কাজ করা যাক, চলো। আজ তো আর তেমন কথা বলা গেল না। খুব ক্লান্ত লাগছে। একদিন জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে।
বলে ছেলেটা একটা ছোট কাগজে ওর নাম্বার আর ঠিকানা দিয়ে বলে উঠল,–একবার ফোন করে চলে আসবে। এখান থেকে খুব কাছেই। পিকুও ওর ঠিকানা কাগজে লিখে দিল। হ্যান্ডশেক করে এবারে ছেলেটা ওর গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।
গাড়িতে উঠেই সুবীরবাবু বলে উঠলেন কি সাংঘাতিক ছেলে রে বাবা ড্যানিয়েল! চাল দিচ্ছিল কি স্পিডে! তুমি ছাড়া আর কেউ দু-মিনিটও টিকতে পারেনি। এক একবার সাইমনের দিক থেকে চোখ সরাই, দেখি ছেলেটা আরেকজনের সঙ্গে খেলতে বসে গেছে। যারা ভালো হয়, সবেতে ভালো হয়।
পিকু যেন শুনে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল। কোথাও কি দেখেছে আগে ছেলেটাকে? একবার জুলির সঙ্গে কথা বলা দরকার।
ও সুবীরবাবুকে বলল,আচ্ছা, মিসেস জুলিকে একবার ফোন করে দেখবেন–কোনও খবর পেয়েছেন কিনা। কাল যখন কথা হল তখন উনি বলেছিলেন যে উনি চেনাজানার মাধ্যমে আপিল করবেন এয়ারক্র্যাশ ইনভেস্টিগেশন ফের চালু করার জন্য।
–হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। একবার ফোন করে দেখি। গাড়ির ড্যাশবোর্ড থেকে জুলির নাম্বার ডায়াল করলেন সুবীরবাবু। ফোনটা অনেকক্ষণ রিং হয়ে গেল। খানিকক্ষণ বাদ দিয়ে আবার ডায়াল করলেন। ফের অনেকক্ষণ রিং হয়ে গেল।
–এত তাড়াতাড়ি তো শুয়ে পড়ার কথা নয়। একবার ওনার বাড়িতে যাওয়া যাবে? পিকু বলে উঠল।
–এখন? রাত নটার সময়?
–হ্যাঁ, গিয়েই দেখা যাক না! আমার মনে হচ্ছে ওনার কিছু বিপদ হয়েছে।
ওরা সুবীরবাবুর বাড়ির প্রায় কাছাকাছি চলে এসেছিল। সুবীরবাবু গাড়ি ঘোরালেন। যখন জর্ডনদের বাড়িতে ওরা পৌঁছোল তখন রাত প্রায় দশটা। বাগানের কয়েকটা আলো জ্বলছে, তবে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় তারা ম্রিয়মান। চারদিকে অনাদরে বেড়ে ওঠা গাছগাছালির ফাঁক দিয়ে বাড়িটাকে দেখলে কেমন রোমাঞ্চ হয়। মনে হয় জীবনের চঞ্চলতা থেকে বহুদূরে একা যেন দাঁড়িয়ে আছে। বাড়ির ভেতরে আলো জ্বলছে। বেল বাজাল ওরা।
আগের দিনও ওনার দরজা খুলতে দেরি হয়েছিল। কিন্তু আজ প্রায় দশমিনিট কেটে গেল। বারবার বেল বাজানো সত্ত্বেও কোনও উত্তর নেই। তাহলে কি জুলি বেরিয়েছেন? কিন্তু। গাড়ি তো গ্যারেজেই! জুলি সেলফোনেও সাড়া দিচ্ছেন না।
বাধ্য হয়ে 911 ডায়াল করলেন সুবীরবাবু। পাঁচমিনিটের মধ্যেই পুলিশ এসে গেল। দরজা খুলে পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে ঢুকে পড়ল ওরা।
জুলি রিক্লাইনারে হেলান দিয়ে নিস্পন্দভাবে বসে আছেন। মুখটা একদিকে কাত। দেখেই বোঝা যায় প্রাণ নেই। সঙ্গে সঙ্গে অ্যাম্বুল্যান্স এসে গেল। ওখানেই ডাক্তাররা ওনাকে মৃত ঘোষণা করল। ঘণ্টা তিনেক আগে জুলি মারা গেছেন। হার্ট অ্যাটাকে।
সুবীরবাবু ও পিকু যখন হাসপাতাল হয়ে বাড়ি ফিরল, রাত তখন তিনটে। গাড়িতে প্রায় একঘণ্টা কেউ কারও সঙ্গে কথা বলেনি।
ঘরে ঢোকার পরে সুবীরবাবুই প্রথমে কথা বললেন।
–যতই বলুক হার্ট অ্যাটাক, আমার সন্দেহ হচ্ছে। কালই ফোনে যখন কথা হল, তখনই উনি বললেন একটা দরকারি জিনিস খুঁজে পেয়েছেন। ডেভের লেখা একটা ছোট নোট। তাতে পাম স্প্রিং বলে একটা জায়গার উল্লেখ ছিল। এটা নাকি নিউইয়র্ক যাওয়ার দু-তিনদিন আগে লেখা। তার নীচে জয়ন্তর নামও ছিল। আমি যখন আরও জিগ্যেস করলাম, উনি ফোনে বলতে দ্বিধা করলেন। বললেন দেখা হলে বলবেন।
–তা আপনি আগে বলেননি কেন?
–তখন কি আর মারা যাবেন বুঝেছি! ভেবেছিলাম দু-একদিনে তো যাবই।…জুলির মৃত্যু সম্বন্ধে তোমারও কি সন্দেহ হয়?
–এটা হার্ট অ্যাটাক নয়। প্লেন অ্যান্ড সিম্পল মার্ডার। আর একটা কথা বলে রাখি। আমরাও ওদের টার্গেট। ওরা যে-কোনওভাবে আসল সত্য লুকোতে চায়। বাবাই-এর রিসার্চ থেকে এয়ারক্র্যাশ–আসল ঘটনা যেন কোনওভাবে প্রকাশ না হয়।
হু! বলে সুবীরবাবু পিকুর দিকে এগিয়ে এসে বললেন, কুছ পরোয়া নেহি। আমি তোমার সঙ্গে আছি। এই ডালরুটির জীবনে আমার এমনিতেই আগ্রহ নেই। রহস্য উদ্ধার করতেই হবে। যে-কোনও মূল্যে।
একটু থেমে সুবীরবাবু ফের বলে উঠলেন,–আরেকটা কথা। আমাকে সব কথা বলো। এই যেমন তোমার ছোটবেলার লুডোর কথাটা আমাকে আগে বলোনি। খুব বড় রহস্য বুঝলে! দাঁড়াও সবগুলো পয়েন্ট একটু একজায়গায় নোট করে নিই।
বলে ডাইনিং টেবিলের ওপর রাখা একটা ছোট নোটবুক বার করে লিখতে থাকলেন।
এক, তোমার লুডোতে কী ভেবে তোমার বাবা ওই দুটো সংখ্যাতে আগে থেকে ক্রশ করলেন। আর তা কী করে মিলে গেল ওনার মৃত্যুর দিনের সঙ্গে!
দুই, ওনার মৃত্যুর পরে কে টাকা পাঠাল ইনোভেটিভ সলিউশনসের নামে।
তিন, তোমার বাবা কেন এত গোপনীয়তার সঙ্গে ওনার আসল পরিচয়টা তোমাদের থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন।
চার, ওনার বন্ধু ডেভ জর্ডন–তিনিও কীভাবে টের পেলেন যে ওনারও সময় ফুরিয়ে আসছে।
পাঁচ, ডেভের লেখা নোটে আসলে কীসের উল্লেখ ছিল। ছয়, জুলির মৃত্যু, জুলি কি কিছু টের পেয়েছিল?
সাত, তুমি ও তোমার দাদা। কেন তোমাকে ঠিক তোমার দাদার মতো দেখতে? উ অনেকগুলো খেয়াল করার মতো পয়েন্ট।
পিকু বলে উঠল–তা লিখছেন যখন–আরও লিখুন। আট-ড্যানিয়েল কী করে আমার নাম জানল?
তাই নাকি? ওই চেস চ্যাম্পিয়ন ছোঁড়াটা?
–হ্যাঁ–খেলতে খেলতে হঠাৎ করে পিকু বলে ফেলেছিল। অন্যমনস্ক হয়ে পিকু ফের বলে উঠল–নয় নম্বর শুধু দাদা নয়। আমার মতো দেখতে আরেকজন কেউ কি আছে? যেমন ড্যানিয়েল বলল। সে-কে?
খানিকক্ষণের নীরবতা কাটিয়ে সুবীরবাবু বলে উঠলেনঃ, জটিল রহস্য। তবে বুঝলেন, ডিটেকটিভ হিসেবে আমি খারাপ নই। কত রাত শার্লক হোমস, ফেলুদা, ব্যোমকেশের বই বুকে জড়িয়ে ঘুমিয়েছি। আর ডিটেকটিভগিরি আমার রক্তেও আছে। আমার এক নিকট আত্মীয় দাদুর মামাতো ভাইয়ের শালা পুলিশের বড় ডিটেকটিভ ছিল। তা আবার ব্রিটিশ আমলের সময়, ভাবো তো! দেখো এ-রহস্যের আমার হাতেই ফয়সালা হবে।
শুতে যাওয়ার সময় পিকু শুনতে পেল নীচের বেসমেন্ট থেকে আওয়াজ আসছে। উঁকি মেরে দেখল সুবীরবাবু ডন বৈঠক দিচ্ছেন। যদিও দুবার করার পরেই তিন মিনিট করে বিশ্রাম।
৪. ডিনার পার্টি
ডিনার পার্টি থেকে বেরিয়ে রবিন গাড়িতে উঠতে যাবে হঠাৎ অফিস নাম্বার থেকে ফোন। রবিন আমেরিকার সেক্রেটারি অফ ডিফেন্স।
লিমুজিনে উঠে বসে ফোনটা ধরল রবিন।
–বলো শেরী। এত রাতে! জরুরি কোনও দরকার আছে?
–খুব ভালো হয় যদি আপনি একবার অফিসে চলে আসেন–একটা জরুরি খবর আছে। বলব?
–আমি গাড়িতে আছি। বলতে পারো।
ল্যাংলে রিসার্চ সেন্টার থেকে IRVE-12 স্পেসক্র্যাক্ট ছাড়ার কথা ছিল। ওটা সাকসেসফুলি লঞ্চ হয়েছে।
এই কথা শোনানোর জন্য জরুরি ফোন? প্রতিমাসে এরকম পাঁচটা ভেহিকল ছাড়া হয়। আর সাম্প্রতিককালে লঞ্চ ফেলিওর হয়েছে এরকম ঘটনাও খুব কম। তবু প্রচণ্ড বিরক্তিটা কথায় প্রকাশ না করে রবিন বলে ওঠেন, পরমাণু বোমা-টোমা লাগানো নেই তো?
–না, না, সেরকম কিছু নয়। এটা হল ইনফ্ল্যাটেবল রি-এন্ট্রি ভেহিকল এক্সপেরিমেন্টের অংশ। অনেক বড় বড় যন্ত্রপাতি এতে করে মহাকাশে পাঠানো যেতে পারে। ম্যাক 20 স্পিডে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে ঢোকার পরও পুড়ে যায় না, গরম হয় না।
একে তো প্রচুর ওয়াইন পার্টিতে খাওয়া হয়ে গেছে–তারপর এসব জটিল জটিল শব্দ– মাথাটা গরম হয়ে যাচ্ছিল রবিনের। বললেন,–তা খুব ভালো। কিন্তু অসুবিধেটা কোথায়?
–এটা ছমাস পরে লঞ্চ হওয়ার কথা ছিল। আজকে লঞ্চ হয়ে গেছে। সাকসেসফুল যদিও।
–বাহ, খুব ভালো খবর। মিশনের সঙ্গে যারা ছিল তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে, নামগুলো কাল পাঠিয়ে দিও। আর কিছু?
–এ মিশনটা নাসার কন্ট্রোলে ছিল না।
–মানে? ল্যাংলে রিসার্চ সেন্টার তো নাসারই আন্ডারে। কী বলছ?
–চারদিন আগে দুজন ছেলে রিসার্চ সেন্টার অ্যাটাক করে এ মিশনের পুরো কন্ট্রোল নিয়ে নিয়েছিল।
–দুজন? নাসার মতো সিকিউরিটি ভেঙে! বলো কি!
–হ্যাঁ, সেজন্যই তো ফোন করছি। আপনি যদি অফিসে আসেন–! ইনফ্যাক্ট বাকি যে কাজ ছিল তা ওরা দুজনে দুদিনেই শেষ করে দেয়। পুরো প্রোগ্রামের কন্ট্রোল নিয়ে নেয়। সেন্টারের ম্যানেজমেন্টের সিনিয়ার লোকেদের হোস্টেজ করে নেয়। একটা আলাদা বিল্ডিং-এ। বন্দি করে রাখে।
–ওরা কতজন ছিল যেন?
দুজন। আগেই তো বললাম।
-বলো কী! শুধু দুজনে? ওখানকার সিকিউরিটি কি করছিল? ঘুমোচ্ছিল? কতজন সিকিউরিটি ছিল ওখানে?
দু-হাজার চারশো। আমাদের দেশের সেরা সিকিউরিটি। নাসার সিনিয়ার ম্যানেজমেন্টকে হোস্টেজ করার সময় ওদের সঙ্গে ছেলেদুটোর সংঘর্ষ হয়। চল্লিশ জন আহত হয়েছে। দুজন মারা গেছে।
বলো কী! এজন্যই অন্য দেশের সঙ্গে যুদ্ধটুদ্ধ মাঝেমধ্যে দরকার। বসে বসে আর খেয়ে খেয়ে সিকিউরিটিগুলো নড়তে চড়তে ভুলে গেছে। যে কটা বেঁচে আছে সবকটাকে ডিসমিস করব।
–ছেলেদুটো নাকি খুব সাধারণ ছিল না। অ্যালিয়েনও হতে পারে।
–কেন অ্যালিয়েন হবে কেন? চারটে মাথা, আটটা পা ছিল নাকি? কীরকম দেখতে ছিল?
না, না, সেরকম কিছু নয়। একদম আমাদের মতো, খুব সুন্দর দেখতে। নীল চোখ, আঁকড়া সোনালি চুল। নাক-মুখ শার্প। দেখলেই গ্রিক দেবতাদের কথা মনে পড়ে যায়।
–তুমি কাদের দলে শেরী? ওদের দলে নয় তো? এত প্রশংসা করছ! মেয়েদের নিয়ে এই সমস্যা। নীল চোখ হোক, লাল চোখ হোক, তা নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। আমার প্রশ্ন, দুজন মিলে এত হাই সিকিউরিটি এরিয়াতে ঢুকে এতগুলো লোককে ভেড়া বানিয়ে কন্ট্রোলটা নিল কী করে?
–ছেলে দুটো নাকি চিতাবাঘের থেকেও জোরে দৌড়োয়। গায়ে অমানুষিক জোর। যে দুজন সিকিউরিটি মারা গেছে, তাদের একজন তো মারা গেছে স্রেফ একটা ঘুষি খেয়ে। যে কোনও কিছু বেয়ে বাঁদরের মতো উঠে যেতে পারে ওরা।
–তা তারা আছে কোথায় এখন? চিড়িয়াখানায়? আর এত যে কথা বলছ,–ওদের স্পেকস-পার্সন হয়ে যাওনি তো?
না, না স্যার। ওরা চলে গেছে। যাওয়ার আগে বলে গেছে যে এটা নাকি ওদের টেস্ট ছিল। রেজাল্ট অবশ্য জানে না। ফেল করলে আবার এরকম কোনও একটা হাই সিকিউরিটি সেন্টারের কন্ট্রোল নিতে হবে।
বলো কী? এরকম কোনও টেররিজমের কোর্স কোনও ইউনিভার্সিটিতে পড়ানো হচ্ছে না তো! তা নাসার কর্তাব্যক্তিরা করছেনটা কী? আমাকে কনফারেন্স করো তো ওখানকার ডিরেক্টারের সঙ্গে।
না, উনি এখন কথা বলবেন না।
–কেন? অভিমান করেছেন না কি?
না স্যার, ওদের মধ্যে একটা ছেলে যাওয়ার সময় ওনার গোঁফটা টেনে ছিঁড়ে নিয়েছে। বলেছে প্রুফ দিতে হবে।
–মাই গড!
ভাবুন! অত সাধের গোঁফ ডঃ ফ্রেডরিক পাফের। তারপর থেকে কথাই বলছেন না।
ফোনটা ছেড়ে গাড়ি থেকেই আরেকটা ফোন করলেন রবিন। CIA-র ডিরেক্টর রবার্টকে।
রবার্ট, তুমি সেদিন কি একটা প্রোজেক্টের কথা বলছিলে না? ইনহিউম্যান লোক তৈরির। কী নাম যেন–প্রোজেক্ট এইচ।
–ইনহিউম্যান নয়, সুপার হিউম্যান বা অতিমানব তৈরির প্রোজেক্ট। অসাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন লোক তৈরির।
কী স্ট্যাটাসে ছিল যেন প্রোজেক্টটা?
–শুনেছিলাম শেষের দিকে। ফাইনাল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।
–কে দেখছে প্রোজেক্টটা?
–সেটাই তো জানি না। সেজন্যই তো ফোন করেছিলাম আপনাকে। আপনার কাছ থেকে যদি কিছু জানা যায়।
–শোনো, একটা ঘটনা ঘটেছে। আমার ধারণা ওটা এই পরীক্ষার সঙ্গে যুক্ত। আমি আধঘণ্টা পরে ভিডিয়ো কনফারেন্স রাখছি। ডিফেন্স অ্যাডভান্সড রিসার্চ প্রোজেক্ট এজেন্সির হেড ডঃ কেভিনকেও ডেকে নিচ্ছি। এই প্রোজেক্টটা আমাদের ইমিডিয়েটলি বন্ধ করার দরকার। জানা দরকার যে কে আসলে এটা নিয়ন্ত্রণ করে। আমরা তিনজনেই যদি না জানি, তাহলে আর কে জানবে? আমেরিকার প্রেসিডেন্ট?
.
১৭.
লাস ভেগাস আর নাসার ল্যাংলে রিসার্চ সেন্টারের ঘটনা দুটোর ভিডিয়ো ফুটেজ বেশ কয়েকবার দেখলেন রবিন। সেক্রেটারি অফ ডিফেন্স রবিনের সন্দেহ নেই যে দুটোই সাধারণ মানুষের কাজ নয়। বিদ্যুৎবেগে এরা যাতায়াত করে। খালি হাতে কংক্রিটের দেওয়াল ভেঙে ফেলে। নির্ভুল লক্ষ্যে পরের পর গুলি চালিয়ে যেতে পারে। এক লাফে পঞ্চাশ ফুট পেরিয়ে যায়। খুব চটপট ঠিক সিদ্ধান্ত নিয়ে নিতে পারে।
ওনার সঙ্গে আজ মিটিং-এ আছেন সিআইএ-র ডিরেক্টর রবার্ট।
–তা আপনার কাছে যা খবর তাতে এসব পরীক্ষা চলছে প্রোজেক্ট এইচ-এর অংশ হিসেবে?
–হ্যাঁ, শুধু এই নয়, কয়েকদিন আগে আমেরিকায় যে পাওয়ার গ্রিড ফেলিওর হয়েছিল, সেটাও নাকি ওরাই ঘটিয়েছিল।
–সেকী? সেবার তো পুরো আমেরিকা পাঁচ ঘণ্টার জন্য অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। নাহ্, এদের এগেনস্টে স্টেপ নিতেই হচ্ছে। তা এসব করে এদের লাভ?
–দেখাতে চায় যে এরাই সেরা মানবজাতি। কুড়িজনেই সারা পৃথিবী দখল করার ক্ষমতা রাখে।
বলো কী?
–শুধু তাই? আমি তো এ-ও খবর পেয়েছি–আপনাকে নাকি কিডন্যাপ করার প্ল্যান আছে।
সর্বনাশ! মেরে-টেরে ফেলবে নাকি?
–না, সেটা অবশ্য জানায়নি। বেঁচে থাকতেও পারেন। তবে এদের কাছে প্রাণের তো বিশেষ দাম নেই। যারা টেস্ট দিতে গিয়ে কয়েকজনকে মেরে ফেলে, তারা পরীক্ষা পাশের পরে কতজনকে মারবে কে জানে!
এই এসি-র ঠান্ডাতেও রবিন রীতিমতো ঘামতে শুরু করলেন।
–তা এই প্রোজেক্ট এইচ চালাচ্ছেটা কে?
–আমি খবর পেয়েছি ডঃ কোলিন বলে একজন। আর্মিতে ছিলেন একসময়। প্রোজেক্টের গোপনীয়তার জন্য যাবতীয় ক্ষমতা ওনার হাতে তুলে দেওয়া হয়।
–ওনাকে জানিয়ে দিন এ প্রোজেক্ট বন্ধ করতে হবে। অবিলম্বে।
–আর যে সব অতিমানবদের অলরেডি সৃষ্টি করা হয়েছে?
–অবশ্যই মেরে ফেলতে হবে।…ওহ, সেদিন এসি চলেনি বলে আমার কুকুরটার যে কী কষ্টই না হয়েছিল! এখনই কোলিনকে ফোন করুন।
–ব্যাপারটা অত সহজে হবে না। মনে রাখবেন এরা প্রত্যেকেই খুব স্পেশাল ক্ষমতা রাখে। অতজন সিকিউরিটি মিলে দুজনকে সামলাতে পারেনি। দেখতে হবে যাতে ওরা কেউ টের না পায়। আমি এমনও শুনেছি যে ওরা সবাই ওদের ওখানে একজনের কথা ছাড়া অন্য কারও কথা শোনে না। এমনকী ডঃ কোলিনেরও নয়।
–কেন? এমন কেন?
–আসলে আর্মির জন্য তৈরি হতো। তা না হলে ওদের মধ্যে ডিসিপ্লিন বোধ আনা যেত না। যে যার ইচ্ছেমতো চললে তো সর্বনাশ। এরা সবাই একজনেরই নির্দেশ শোনে।
–হুঁ বুঝলাম। তা তার সঙ্গেও কথা বললো তাহলে। মোদ্দা কথা এ প্রোজেক্ট ইমিডিয়েটলি বন্ধ করতে হবে। আমাকে কিডন্যাপ কী সর্বনেশে কথা!
.
১৮.
কী বলবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না ডঃ কেন। একটা সময়ে উনি এ প্রোজেক্টে অংশগ্রহণ করতে চাননি। চাননি অতিমানব তৈরি করতে। উনি জানতেন এর বিপদ। একবার তৈরি করার পর এদের নিয়ন্ত্রণ করা খুব কঠিন। কারণ এরা বুদ্ধির দিক থেকেও সাধারণ মানুষের থেকে অনেক এগিয়ে। বলার আগেই বুঝে যায়।
কিন্তু উপায় ছিল না। ওনার বিরুদ্ধে টেররিজমের চার্জ আনা হয়েছিল। তার থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় এই প্রোজেক্টের চিফ সায়েন্টিস্ট হওয়া। সবাই জানত যে জিন নিয়ে ছেলেখেলা যদি কেউ করতে পারে–সে একজনই, ডঃ কেন। কীভাবে মানুষের জিনের মধ্যে পরিবর্তন এনে তাকে স্পেশাল ক্ষমতা দেওয়া যায় সে প্রযুক্তি শুধু ডঃ কেনেরই জানা ছিল। আর এটাই সর্বনাশ ডেকে আনল। ষড়যন্ত্রের শিকার হলেন। আর এই ষড়যন্ত্রের জাল পাতল কে? আর কেউ নয়, স্বয়ং গভর্নমেন্ট। যে সে গভর্নমেন্টও নয়, সব থেকে শক্তিশালী রাষ্ট্রের গভর্নমেন্ট। এ ধরনের জাল থেকে চেষ্টা করলেও একজনের একার পক্ষে বেরোনো সম্ভব নয়।
আর ভাগ্যের কী পরিহাস! আজ সেই গভর্নমেন্টই আদেশ দিয়েছে তার সব সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দিতে। এরা কি একটা মাটির পুতুল যে তৈরি করলাম আর ভেঙে দিলাম! এরা প্রত্যেকেই ডঃ কেনের সন্তানের মতো। এরা ডঃ কেনকেই এদের বাবা বলে জানে। এরা ছোটবেলায় ডঃ কেনের কাছে গল্প না শুনে ঘুমোতে যেত না। সকালে ডঃ কেনের সঙ্গে বসে প্রার্থনাসঙ্গীত না গাইলে এদের ভোর শুরু হত না। এরাই বিস্ফারিত চোখে, মুখে খাবার নিয়ে বসে থাকত, আর ডঃ কেনের তাসের ম্যাজিক দেখত। এদের কারও জ্বর হলে ডঃ কেনই মাঝরাতে বারবার এসে কপালে হাত দিতেন। রাত জেগে বসে থাকতেন। আর এদেরকেই মেরে ফেলতে হবে?
প্রোজেক্ট ডাইরেক্টর ডঃ কোলিন খানিক আগেই ওপরতলার আদেশ শুনিয়েছেন। উনি প্রতিরোধের যাবতীয় চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু আদেশের কোনও নড়চড় হয়নি। আজকের মধ্যেই এ কাজ সারতে হবে। এ ল্যাবও বন্ধ করে দিতে হবে।
ঝাপসা চোখে বিল্ডিংটা একবার শেষবারের মতো পর্যবেক্ষণে বেরোলেন ডঃ কেন। চারতলা। বেসমেন্টে নানান ধরনের জন্তু রাখা। চিতাবাঘ থেকে গিরগিটি। ইঁদুর থেকে র্যাটল স্নেক। এদের থেকে ডিএনএ নিয়ে নানান ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়। এদের ওপরেও অনেক টেস্ট হয়। এর পাশেই বিশাল অপারেশন থিয়েটার। বিশাল স্টেনলেস স্টিলের ফার্মেন্টর, সাইক্লোট্রন–জিন পরিবর্তনে যে রেডিয়ো অ্যাকটিভ কণা লাগে তার জন্য।
একতলায় NMR স্ক্যানার। PET স্ক্যানার। অত্যাধুনিক মাইক্রোবায়োলজি ল্যাব। ডঃ কেনের নিজের হাতে খুব যত্নে তৈরি করা। দোতলায় বিশাল ল্যাবরেটরি–এখানেই জিনের গঠন পালটানোর নানান ধরনের যন্ত্রপাতি। তিনতলায় লাইব্রেরি। সার দিয়ে কম্পিউটার রাখা আছে। অফিস এরিয়া। বিশাল অডিটোরিয়াম।
ধীরপায়ে পুরো অফিসটা ঘুরে ডঃ কেন অডিটোরিয়ামে ঢুকলেন। ওনার তৈরি সব অতিমানবকে উনি অডিটোরিয়ামে আসতে বলেছেন দু-ঘণ্টা বাদে। এখন অবধি কেউ কিছু জানে না। আর দু-ঘণ্টা বাদে এই অডিটোরিয়ামই হবে ওদের বধ্যভূমি। ওদের প্রত্যেককে ইঞ্জেকশন দিতে হবে। কৃত্রিমভাবে তৈরি ক্ষতিকারক ভাইরাসের ডিএনএ এদের ক্রোমোজোমে মিশে যাবে। তারপর আর কতক্ষণ?
মুখে হাত চাপা দিয়ে অন্ধকার অডিটোরিয়ামের প্রথম সারিতে বসে গেলেন ডঃ কেন। কান্নায় ভেঙে পড়লেন। এদের কী বলবেন? তোমাদের জীবন আমিই দিয়েছি, আজকে সে জীবন আমিই আবার কেড়ে নেব।
তিলতিল করে যত্নে গড়ে তোলা এই প্রাণগুলোকে কালকের ভোর কোনওভাবেই দেখতে দেওয়া যাবে না। আর ওরা? ডঃ কেন জানেন যে ওরা এর কোনও প্রতিবাদ করবে না। ওদের কাছে একটাই পৃথিবী–একটাই সূর্য–একটাই ঈশ্বর–একজনই শেষ কথা–তিনি হলেন ডঃ কেন। সেরা সৈনিকদের মতো হাসিমুখে মৃত্যুও মেনে নেবে আদেশ পেলে।
কতক্ষণ এভাবে কাঁদছিলেন কে জানে? বাইরের বন্ধ দরজায় টোকা পড়ছে। ল্যাবের টিম ইঞ্জেকশন রেডি করে এসে গেছে। প্রথম সারির চেয়ার থেকে দরজার দিকে হেঁটে এগিয়ে গেলেন ডঃ কেন। মাঝের কুড়ি ফুটকে ওনার মনে হল যেন কুড়ি বছর পেছনে হাঁটা।
স্পষ্ট কানে ভাসছে অনেকগুলো বাচ্চার কান্না। প্রথম ভোরের আলো ছড়িয়ে পড়েছে ওদের ছোট ছোট শরীরে, হাতে-পায়ে। আর তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন উনি। না, এরা তো শুধু নিজের সৃষ্টি নয়–কোনও এক্সপ্রেরিমেন্টের ফসল নয়–এরা তো ডঃ কেনেরই সন্তান। মনে মনে ডঃ কেন তখনই স্থির করেছিলেন সুখে-দুঃখে সবসময় এদের সঙ্গে থাকবেন উনি। বাবা-মার আরও নানান পরিচয়ের শূন্যস্থানগুলো একাই পূরণ করবেন উনি। আর আজকে? আজকে সে প্রতিজ্ঞা ভাঙতে হবে–খুনি হতে হবে। ওরা যখন ছটফট করবে যন্ত্রণায়, তখনও মনকে বোঝাতে হবে–যা এতদিন ভেবেছি সব মিথ্যা সব অহেতুক প্রশ্রয়। এরা সন্তান নয়– কেউ নয়। বিজ্ঞানীর জীবনে সত্য শুধু একটাই বিজ্ঞান।
.
১৯.
স্যার, ওরা সব অডিটোরিয়ামে এসে বসেছে। আমাদের মেডিকাল টিমও রেডি। আপনি কি একবার ওদের সঙ্গে কথা বলবেন? শেষবার?
শেষবার কথাটা খুব কানে লাগল ডঃ কেনের। না–বিরক্ত হয়ে স্বভাববিরুদ্ধ ভাবে জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন ডঃ কেন। তারপর কি ভেবে আবার উঠে দাঁড়ালেন। বলে উঠলেন– চলো।
খানিক আগে অডিটোরিয়াম ছেড়ে চলে এসেছিলেন। মেডিকাল টিমের প্রস্তুতি–একবার দেখে নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন। এসে বসেছিলেন ওনার চেম্বারে–তখন ওদের কেউ ছিল না।
ধীরপায়ে ডঃ কেন এগিয়ে চললেন অডিটোরিয়ামের দিকে। সঙ্গে জুনিয়র সায়েন্টিস্ট ডক্টর রজার। ঢোকার সঙ্গে-সঙ্গেই পরিচিত সমবেত কণ্ঠ–গুড মর্নিং ডক্টর কেন। অন্যদিনের মতো একইভাবে ফিরতি গুডমর্নিং–বলতে গিয়ে আওয়াজ বেরোল না ডঃ কেনের। ডায়াসের ওপর উঠে নিষ্প্রাণ কণ্ঠে বলতে শুরু করলেন–
–আমি সরাসরি আসল কথায় চলে আসি। তোমরা হয়তো আগেই খানিকটা আন্দাজ পেয়েছ। হা–আজকেই তোমাদের শেষ দিন। খানিকক্ষণের মধ্যেই তোমাদের ইঞ্জেকশন দেওয়া হবে। আর তার দশমিনিটের মধ্যেই তোমাদের মৃত্যু হবে। যন্ত্রণা খুব একটা হবে না হলেও তা সহ্য করার শক্তি তোমাদের আছে। ইঞ্জেকশন দেওয়ার সময় তোমরা মেডিকাল টিমের সঙ্গে সবরকম সহযোগিতা করো। কারও কোনও প্রশ্ন আছে?
পুরো অডিটোরিয়ামে পিন ড্রপ সাইলেন্স। একেই বলে ট্রেনিং। একেই বলে শৃঙ্খলাবোধ। এদের কি আর কষ্ট হচ্ছে না! এ জীবনের প্রলোভন কাটানো বড় শক্ত। সেই আবেগ-অনুভূতিকে সহ্য করার ট্রেনিং পেয়েছে এরা! কিন্তু ডক্টর কেন তো আর এদের মতো ট্রেনিং নেওয়া সেনা নন। তাই এই নীরবতা ওনার সহ্য হল না। উনি ফের বলে উঠলেন,আমি তোমাদের খুব ভালোবাসি। তোমরাই ছিলে আমার সবথেকে আপনার। তোমাদের প্রত্যেককে আমি আমার সন্তানের মতো দেখেছি। কিন্তু এই মুহূর্তে এটাই আমার আদেশ। আরেকবার জিগ্যেস করছি– কারও কোনও প্রশ্ন আছে? ধরা গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন।
একটা হাত উঠেছে। কোলিন। ডক্টর কেন সবাইকে সমানভাবে ভালোবাসার চেষ্টা করলেও, যাদেরকে একটু বেশি ভালোবাসতেন, তাদের মধ্যে কোলিন একজন। খুব শান্ত-বাধ্য ছোটবেলা থেকেই। ছোটবেলায় মাঝেমধ্যেই পালিয়ে ডক্টর কেনের ঘরে চলে আসত। আর ডক্টর কেনের গা ঘেঁষে বসে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ডক্টর কেন কি করেন তা লক্ষ্য করত। হাজারো প্রশ্ন করত। কখনও-বা রাতে ভয় পেয়ে ডক্টর কেনের চাদরের মধ্যে ঢুকে ডক্টর কেনকে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ত।
ডক্টর কেন–আপনি যে বলতেন আমাদের জীবন খুব মূল্যবান। আমরা কখনও যেন তা অহেতুক নষ্ট না করি। কিন্তু আজ হঠাৎ করে আমাদের মৃত্যুর আদেশ। খানিকক্ষণ থেমে কোলিন ফের বলে উঠল–আমরা কি একসপ্তাহ সময় পেতে পারি?
না কোলিন–আজকেই–পরের একঘণ্টার মধ্যে এ বিল্ডিং-এর সব আলো নিভে যাবে। তোমাদের তৈরিই করা হয়েছিল যুদ্ধের সেনা হিসেবে। সেনাদের তো মৃত্যু যখন-তখনই আসে। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে তাদের মৃত্যুবরণ করতে হয়। একটু থেমে ডঃ কেন ফের বলে উঠলেন, আমায় তোমরা পারলে ক্ষমা করো।
তারপর মাথা নিচু করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। ঘাড় ঘোরালে দেখতে পেতেন ঘরের সবাই যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে উঠেছে তাদের প্রিয় দেবতাকে শেষবারের মতো সম্মান জানাতে।
.
২০.
পিকুর ঘুম খুবই পাতলা। তাই দরজায় একটা টোকাতেই ধড়ফড় করে উঠে পড়ল। ঘড়িতে ভোর পাঁচটা। তিন ঘণ্টা হল ঘুমিয়েছে। দরজায় সুবীরবাবু ড্রেসিংগাউন পরে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে চিন্তার ছাপ।
কী ব্যাপার কাকু? এত সকালে?
–আমার বাগানে কীসের আওয়াজ পেলাম। উঠে বেরোতে যাব, দেখি ফোনে মেসেজ এসেছে, পড়ে দ্যাখো।
ফোনটা হাতে নিয়ে দেখল পিকু,–লিভ অ্যান আবার ইমিডিয়েটলি।
সুবীরবাবু বললেন,–তোমার জন্য মেসেজ বুঝতেই পারছ। কেউ তোমার এখানে থাকা পছন্দ করছে না। এক্ষুনি অ্যান আর্বার ছাড়তে বলছে।
কাকু, আমি এ-বাড়ি ছেড়ে এখনই বেরিয়ে যাব। আমার জন্য আপনিও বড় বিপদে পড়েছেন, আমিই এরজন্য দায়ী।
সুবীরবাবু এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন পিকুকে।
–আমার যদি তোমার মতো ছেলে হত, আমি নিজেকে সত্যি ভাগ্যবান মনে করতাম পিকু। আমার বিশ্বাস আসল সত্যের সন্ধান তুমি খুব তাড়াতাড়ি পাবে। সেটা ভালো বা খারাপ যেটাই হোক। আর আমার বিপদ নিয়ে একদম ভাববে না। গত পনেরো বছর ধরে আমার জীবন কীরকম জানো তো? কোনও বৈচিত্র্য নেই, কোনও চ্যালেঞ্জ নেই। কথা বলার কোনও লোক নেই। অনেকসময় জীবন এত বিবর্ণ হয়ে যায় যে থাকা আর না থাকা একই ব্যাপার।
এই যে তোমার সঙ্গে এতদিন বাদে কথা বলতে পারছি, মনে হচ্ছে যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছি।
একটু থেমে সুবীরবাবু আবার বললেন, আমার ব্যাপারে ভয় পেয়ো না। আমার গায়ে কিন্তু অসম্ভব জোর। একবার এখানে দশটা গুন্ডাকে একা পিটিয়েছিলাম।
পিকুকে হাসতে দেখে সুবীরবাবু যেতে যেতে বললেন,–আহা! মারপিটের সময় কি আর কেউ কাউন্ট করে দেখে কজন আছে! তবে একাধিক লোক ছিল তাতে সন্দেহ নেই। আমি এবার একটু বাইরের আওয়াজের ব্যাপারটা দেখে আসি। কীরকম একটা অস্বাভাবিক পড়ে যাওয়ার আওয়াজ পেয়েছিলাম।
দাঁড়ান কাকু, আমিও যাচ্ছি।
চলো!
পোশাক পরে দুজনে বাইরে বেরিয়ে এল। আকাশ একটু লালচে হতে শুরু করেছে। পাশের কোনও একটা গাছের থেকে কাঠঠোকরার ঠুকঠুক আওয়াজ আসছে। বাতাসে এখন শীতের আমেজ। পাতলা চাদরে গা ঢাকা দেওয়ার মতো ঠান্ডা। সুবীরবাবুর বাড়িটা অনেকটা জায়গা জুড়ে। প্রথমেই ওরা গেটের দিকে এগিয়ে গেল বাড়িতে ঢোকার রাস্তা দিয়ে, সেখানে কাউকে দেখতে পেল না। ঘাসের লন পেরিয়ে দূরের পুকুরের দিকটাও ঘুরে দেখে এল। নাহ, কিছুই নেই! রান্নাঘরের পাশ দিয়ে সারি সারি ম্যাপল গাছ। ওখান দিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল পিকু।
–ওটা কী?
ছুটে কাছে গেল ওরা। উপুড় হয়ে পড়ে আছে একজন। মুখটা একপাশে ঘোরানো। গায়ের সবুজ শার্টে স্পষ্ট রক্তের ছোপ। গায়ের রংও অদ্ভুত সবুজ। তাই ঘাস ঝোপে সত্যিই চট করে চোখে পড়ে না। কেউ পিছন থেকে গুলি করেছে। লোকটার বাঁ-হাতে একটা রিভলভার।
–চিনতে পেরেছেন? পিকু জিগ্যেস করল।
বিস্ময়ে বিমূঢ় সুবীরবাবু বলে উঠলেন,না, ভালো করে মুখটা দেখা যাচ্ছে না তো! কে বলো তো? এরকম সবুজ রং কারো হয় না দেখলে বিশ্বাস হত না!
–সেদিন যে ছেলেটা চেস টুর্নামেন্টে জিতল, সেই ছেলেটা।
–বলো কী? ওই ভালো স্টুডেন্ট? শিওর? রংটা ওরকম সবুজ হল কী করে?
–কে জানে? তবে এটা যে ওই ছেলেটাই তাতে সন্দেহ নেই। গায়ে হাত দেওয়ার দরকার নেই। আপনি 911 ডায়াল করুন। পুলিশ এসে দেখুক।
সুবীরবাবু ফোন করার খানিকক্ষণের মধ্যে পুলিশ এসে গেল। অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হল ছেলেটাকে। তবে তখনই চেক করে বলে দিলেন যে প্রাণ নেই। পুলিশ গায়ের রং দেখে মুখে কিছু না বললেও সবাই অবাক। সেই একই পুলিশের ডিটেকটিভ এসেছে সঙ্গে। ওদের দেখেই চিনতে পেরে বলে উঠল,–পরশু রাতে জুলি জর্ডনের ওখানে দেখা হয়েছিল না? আপনারাই তো ডেকেছিলেন!
একটু থেমে ফের বলল, ফরেন্সিক এক্সপার্ট আসবে এক্ষুনি। এ জায়গাটা সিল করে দেওয়া হবে। আপনারা বাড়ি ছেড়ে কোথাও বেরোবেন না ক্লিয়ারেন্স না পাওয়া অবধি। আচ্ছা, আপনারা কি ছেলেটাকে চিনতেন?
সম্মতি জানিয়ে পিকু মাথা নাড়ল,–পরশু ওপেন চেস টুর্নামেন্টে একসঙ্গে খেলেছিলাম। ও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। সেই সূত্রে পাঁচ মিনিটের আলাপ।
ডিটেকটিভ আরও বেশ কিছু প্রশ্ন করল। এখানে আগে কখনও ছেলেটাকে দেখা গেছে। কিনা, এখানে আসার কোনও কারণ থাকতে পারে কিনা ইত্যাদি।
সব কথা শুনে রীতিমতো ভুরু কুঁচকে চলে গেল অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে।
সুবীরবাবু পাশ থেকে বললেন,–চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল তা না বললেই পারতে। এখানকার পুলিশ অসম্ভব বোকা। কমনসেন্সের প্রচণ্ড অভাব। মনে মনে ভাবছে তুমি টুর্নামেন্ট হারার জন্য মার্ডার করেছ কিনা!
সুবীরবাবুর কথাই ঠিক। ডিটেকটিভ আবার ফিরে এসে খুব গম্ভীরভাবে পিকুকে জিগ্যেস করল,–খেলার শেষে তোমাদের মধ্যে কি মারপিট বা ঝগড়া হয়েছিল?
পিকু হেসে বলল, না, না। আমরা চেস খেলছিলাম, আমেরিকান ফুটবল বা রাগবি নয়।
ডিটেকটিভ কী বুঝল কে জানে? এবার পুরো দলবল নিয়ে চলে গেল আশেপাশে খোঁজ নিতে–কেউ কোনও সন্দেহজনক কিছু দেখেছে কিনা। গেটের কাছে একজনকে আর ক্রাইমের জায়গাটায় আরেকজনকে দাঁড় করিয়ে চলে গেল।
এরমধ্যে সুবীরবাবুর ফোন বেজে উঠল। সাইমনের ফোন। সেই মিসিগান লস্কুলের লাইব্রেরিয়ান–যার সঙ্গে চেস টুর্নামেন্টের দিন দেখা হয়েছিল, যিনি পিকুকে জড়িয়ে ধরে তিনমিনিট কেঁদেছিলেন।
একবার গেটে আসবেন? আপনার গেটে যে গাধাটি দাঁড়িয়ে আছে, সেটি আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে না।
–আরে আপনি! আমি এক্ষুনি আসছি।
গেটের কাছে ভদ্রলোকের সাদা মার্সেডিজ গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। উনি ড্রাইভারের সিটে বসে হাত নাড়ছেন। সুবীরবাবু বলার পর রোবট পুলিশ সাইমনকে ঢুকতে দিল। গাড়ি সোজা গ্যারেজে ঢুকিয়ে ভদ্রলোক গাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন।
সুবীরবাবুর কৌতূহলী মুখের দিকে তাকিয়ে গ্যারেজ থেকে বাড়িতে ঢোকার দরজা দেখিয়ে বলে উঠলেন, সব জানি। ভেতরে ঢুকে বলছি।
ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বলে উঠলেন, পিকু, তুমি দু মিনিটের মধ্যেই রেডি হয়ে বেরিয়ে যাও। তোমার খুব বড় বিপদ। রাস্তায় কুড়ি ফুট অন্তর ক্যামেরা রাখা আছে। পুলিশ ওইসব ক্যামেরার ছবি চেক করছে। এ রাস্তা দিয়ে গত তিনঘণ্টায় যত গাড়ি গেছে, সব গাড়ি ও গাড়ির ভেতরের লোকেদের ছবি–ওই সব ক্যামেরায় তোলা আছে। এই সময় এমনিতেও খুব কম গাড়ি যায়, তাই খুঁটিয়ে দেখছে ওরা।
–তাতে কী?
–তাতে পিকুর ছবি আছে।
-মানে? সে তো আমরা পরশু মাঝরাতে একটা জায়গা থেকে ফিরছিলাম বলে। আমিও তো ছিলাম গাড়িতে। সুবীরবাবু বললেন।
তা নয়। ঠিক পিকুরই মতো দেখতে আরেকজন আছে। তার ছবিই ধরা পড়েছে ক্যামেরাতে। তার হাতেই খুন হয়েছে ওই ছেলেটা। যে মারা গেছে তার নাম ড্যানিয়েল। পরশু দিনই আমি আপনাদেরকে ড্যানিয়েল সম্পর্কে বলতাম। ও কাছাকাছি ছিল বলে বলিনি। ড্যানিয়েল ঠিক সাধারণ মানুষ ছিল না, ও ছিল অনেক স্পেশাল ক্ষমতার অধিকারী। ও আর ওর বন্ধু থাকত আমার পাশের বাড়িতে। তাই আমি ওদের দুজনের সম্পর্কেই খানিকটা জানতাম।
একটু থেমে পিকুর দিকে তাকিয়ে সাইমন বলে উঠলেন,–আমি সেদিন শুধু শুধু অতটা কঁদিনি। তোমার বাবা ছিলেন আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ও মিসিগান মেডিক্যাল স্কুলে বায়োমেডিক্যাল সায়েন্স রিসার্চ বিল্ডিং-এ রিসার্চ করত। আমরা প্রায়ই বসে দাবা খেলতাম। আগে আমি বলিনি, কারণ ড্যানিয়েল অনেক দূর থেকেও সব কথা শুনতে পায়। দেখতে পায়। টুর্নামেন্টের শুরু থেকেই ও তোমাকে বিশেষভাবে লক্ষ করছিল। ওর দৃষ্টিতে তোমার ওপর একটা আক্রোশ ছিল–সেটা আমার চোখ এড়ায়নি।
–দুদিন আগে আমি জুলি জর্ডনের বাড়ি গিয়েছিলাম, ওখানে ওকেই আমি দেখেছিলাম, আমার মনে হয় ও আমাকে দেখেছিল। পিকু ফের বলে, পরশুদিন ও আমার অ্যাড্রেস-ও নিয়েছিল।
–হ্যাঁ, তাই হবে। জুলিকে আমিও চিনতাম, কারণ ওর হাজব্যান্ড ডেভের সঙ্গে আমার। পরিচয় ছিল। কাল মাঝরাতে ড্যানিয়েলকে আমি বেরোতে দেখি। ওর হাতের বন্দুকটা আমার চোখে পড়েছিল। কেন জানি না, তোমার কথাই মনে হয়েছিল। একটু দূরে দূরে থেকে ফলো করছিলাম। গাড়িটা একটু দূরে রেখে তোমাদের পিছন দিকে যে বাড়িটা আছে, দেখলাম, তার মধ্যে দিয়ে তোমাদের বাড়ির দিকে এগোচ্ছে। ঠিক এর মধ্যে আরেকজনকে দেখলাম ওর পিছু নিতে। অন্ধকারে তাকে আমি অবশ্য ভালো করে দেখতে পাইনি।
ঠিক করলাম ওখানেই অপেক্ষা করব। মিনিট পাঁচেক কেটে গেল। হঠাৎ একটা আওয়াজ পেলাম তোমাদের বাগানের দিক থেকে। যাব কি যাব না ভাবছি, দেখলাম পিকু তোমাদের পেছনের বাড়ির বাগান থেকে জোরে হেঁটে বেরিয়ে আসছে।
আমি স্বাভাবিক ভাবেই ওর দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম। ছেলেটা বলে উঠল, আমি পিকু নই, পিকুকে এক্ষুনি অ্যান আবার ছেড়ে চলে যেতে বলুন।
বলে পকেট থেকে একটা খাম বার করে এগিয়ে দিল। একটা গাড়ি দেখিয়ে বলে উঠল, আমি ওর জন্য এখানেই অপেক্ষা করছি। ওর বড় বিপদ।
এটা আধঘণ্টা আগের কথা। পুলিশ এসে যাওয়ায় আমি আগে বলতে পারিনি।
–কিন্তু কোথা দিয়ে বেরোব? গেটে তো পুলিশ আছে।
–আরে সে তো সামনের গেটে। তুমি এই পেছনের বাগান পেরিয়ে পেছনের বাড়ির মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলে যাও।
–কিন্তু ছেলেটা কে?
–ছেলেটা তোমার যমজ ভাই। তুমি নিশ্চিন্তে ওর সঙ্গে যেতে পারো। ও তোমাকে বাঁচাতেই এসেছে, জয়ন্ত আমার খুব বন্ধু ছিল বলেই ব্যাপারটা জানি। শান্তনু, অর্থাৎ তোমার দাদা মারা যাওয়ার পর ওর ডিএনএ দিয়ে দুজন যমজ সন্তানের পরিকল্পনা করেছিল জয়ন্ত। একজন হলে তুমি। অন্যজন নির্ঘাত ওই ছেলেটা। যাও পিকু, আর একমুহূর্তও দেরি কোরো না।
পিকু ব্যাগ নিয়ে পাঁচ মিনিটে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সাইমনের কথামতো বাড়ির পিছন দিক দিয়ে অন্য বাড়ির বাগান পেরিয়ে পিছনের রাস্তায় গিয়ে নামল। বাইরে এখন ভালো আলো। সূর্যোদয় হয়ে গেছে। একটা কালো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ির দিকে এগিয়ে যেতেই দরজা খুলে গেল।
পিকু ওঠামাত্র গাড়িতে বসে থাকা লোকটা গাড়ি স্টার্ট দিল। ওর মুখ দেখে অবাক হয়ে গেল পিকু। এ যেন নিজেকেই আয়নায় দেখছে। গাড়ি চালাতে চালাতেই ছেলেটা বলে উঠল,–দেখতে এক হলে কী হবে, আমার নামটা কিন্তু একদম অন্যরকম। ব্রায়ান। চট করে। কয়েকটা দরকারি কথা বলে নিই। সাইমনের হাতে একটা খাম পাঠিয়েছিলাম। ওর মধ্যে একটা প্লেনের টিকিট আছে। আর পাম স্প্রিং-এর একটা ঠিকানা আছে। ওই ঠিকানায় কাল সকাল ছটায় আমরা মিট করব। তুমি যে প্রশ্নের খোঁজে এসেছ, সে প্রশ্নের উত্তর ওখানেই পাবে।
একটু থেমে ব্রায়ান একবার সাইড মিররে তাকিয়ে নিয়ে বলল,–যা ভয় পেয়েছিলাম। তাই দেরি হয়ে গেছে। ফলো করছে।
–কে পুলিশ?
না, না, পুলিশ হলে তো সোজা ছিল। এ হল ড্যানিয়েলের বন্ধু। খুব বিপজ্জনক। ও তিন মিটার অব্দি হাইজাম্প দিতে পারে। আট সেকেন্ডে একশো মিটার ছুটতে পারে। তা, তুমি কি গাড়ি চালাতে জানো?
-কেন?
–তুমি চালাও। আমি ওকে গুলি চালিয়ে থামানোর চেষ্টা করি।
–কিন্তু আমার যে ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই এখানকার।
জোরে হেসে উঠল ব্রায়ান,–আগে তো প্রাণ বাঁচাও, তারপরে নিয়ম।
গাড়ি চালু অবস্থাতেই ড্রাইভিং সিটে কোনওরকমে চলে এল পিকু। বলল,–কোনদিকে এয়ারপোর্ট?
–আরে যে-কোনওদিকে যাও। স্পিডটা শুধু দেড়শোর কম কোরো না, আর পুলিশের গাড়ি দেখলেও দাঁড়িও না।
পিকু আগে গাড়ি চালিয়েছে, কিন্তু ভারতে আর আমেরিকাতে চালানোর মধ্যে অনেক তফাত। তবু এখন একটাই নিয়ম। ধাক্কা বাঁচিয়ে ম্যাক্সিমাম স্পিড। করলও তাই। ট্রাফিক কাটিয়ে ঝড়ের বেগে গাড়ি চালাতে লাগল–ঠিক ভিডিয়ো গেমসের মতো। ওর রিফ্লেক্স এমনিতেও খুব ভালো।
জানলা থেকে হাত বাড়িয়ে ব্রায়ান পিছনে তাড়া করে আসা গাড়িটাতে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে। পিছনের গাড়ির ড্রাইভারও বেশ ওস্তাদ। ডানদিক-বাঁদিক কাটিয়ে এমনভাবে চালাচ্ছে। যে গুলি করা খুব শক্ত। আর এর মধ্যেই পিকুর গাড়ির খুব কাছে চলে এসেছে।
ব্রায়ানের হাত বেশ পাকা। খানিকবাদেই তাড়া করে আসা গাড়িটার ডান দিকের টায়ারে গুলি লাগল। গাড়িটা কাছে চলে এসেছিল। ওই ছেলেটাও গুলি চালাতে শুরু করেছে। কয়েকটা গুলি ব্রায়ানের গাড়িতে এসেও লেগেছে। ব্রায়ানও এখন ছেলেটাকে লক্ষ্য করে গুলি চালাচ্ছে।
হঠাৎ ব্রায়ান চেঁচিয়ে বলে উঠল, বুকে গুলি লেগেছে ছেলেটার। তবে তাতে ওর কিছু হবে কিনা বলা শক্ত। আমার গাড়ির কাঁচ বুলেট প্রুফ বলে বাঁচোয়া।
পিছনের গাড়িটা থেমে গেছে। ব্রায়ান চেঁচিয়ে উঠল, দাঁড়িও না। জোরে চালিয়ে যাও।
এয়ারপোর্টে পিকুকে ড্রপ করে ব্রায়ান বলল,সাবধানে যেও। পাম স্প্রিংস-এ দেখা হবে। ড্যানিয়েলের বন্ধুকে আমি একটু সামলে আসি। ও জানে যে আমরা কোথায় যাচ্ছি। বেঁচে থাকতে কোনওভাবে সেটা ও হতে দেবে না। গুলি লেগেছে ঠিক, কিন্তু মরেছে কিনা তা দেখে আসি।
পিকু হাঁ করে দাঁড়িয়েছিল, ব্রায়ান বলল,–শিগগির ভেতরে ঢুকে যাও। তুমি আমার জন্য চিন্তা কোরো না। আমি তোমার মতো সাধারণ নই। আমি লড়তে শিখেছি। ব্রায়ান জোরে গাড়ি চালিয়ে দিল আবার।
৫. ডেট্রয়েট থেকে লস অ্যাঞ্জেলেস
ডেট্রয়েট থেকে লস অ্যাঞ্জেলেস। লস অ্যাঞ্জেলেস থেকে পাম স্প্রিংস মোটে আধঘণ্টার ফ্লাইট। মাঝে অবশ্য একঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়েছে। পাম স্প্রিংস-এ ফ্লাইট থেকে বেরিয়েই পিকু দেখল এক্সিট গেটের পাশে ট্যাক্সি বুকিং বুথ। বোর্ডিং পাস স্ক্যান করে, কত সময় বাদে ট্যাক্সি লাগবে বললেই ঠিক সেই সময়ে ট্যাক্সি এসে যাবে। রাত আটটা বাজে। সাড়ে আটটায় ট্যাক্সি বুক করে লাগেজ নেওয়ার জন্য এগোল পিকু। লাগেজ নিয়ে বেরোতে বেরোতে আটটা কুড়ি। এয়ারপোর্টটা ছোট। মরুভূমির মধ্যে বানানো শহর। বিত্তবানদের থাকার জায়গা। গরমে তাপমাত্রা পঞ্চাশ ডিগ্রি ছোঁয়। এখন অবশ্য গরম তেমন পড়েনি। বিশেষ করে সন্ধেবেলা বলে বেশ হাওয়া বইছে। দূরে মরুভূমির মধ্যে মাথা উঁচু করা ছোট ছোট পাহাড় দেখা যাচ্ছে। আর সে পাহাড়ের সঙ্গে পড়ন্ত সূর্যের আলোয় লুকোচুরি খেলছে মেঘে ভাসা নীল আকাশ।
ঠিক সাড়ে আটটায় ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল পিকুর সামনে। বুকিং-এর সময়ে যে ট্যাক্সি নাম্বারটা পেয়েছিল, সেই নাম্বারটা মিলিয়ে ট্যাক্সির পিছনে লাগেজ রেখে ভেতরে উঠে বসল। ট্যাক্সি ড্রাইভার একটু উদ্ধতই হবে, কারণ লাগেজ গাড়িতে তোলার ব্যাপারে কিছুমাত্র সাহায্য করল না।
পিকুকে ব্রায়ান যে খামটা দিয়েছিল, তার মধ্যে এয়ার টিকিট ছাড়াও হোটেল বুকিং আর আগামীকাল কোথায়, কটায় দেখা করবে তার ডিটেলস ছিল। সেই হোটেলের অ্যাড্রেসই ট্যাক্সি ড্রাইভারকে দিল পিকু। কোনও কথা না বলে অ্যাড্রেসটা নিয়ে লোকটা গাড়ির ড্যাশবোর্ডে টাইপ করতে গাড়ি ছুটে চলল মরুভূমির বুক চিরে প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে।
রাস্তার দুধারে কী আছে তা অন্ধকারে স্পষ্ট বোঝা না গেলেও এটুকু পিকু বুঝতে পারল যে আশেপাশে জনবসতি নেই। গাড়ির আলোতে যেটুকু দেখা যাচ্ছে তা হল দু-ধারে প্রসারিত মরুভূমি আর ছোট ছোট ক্যাকটাস জাতীয় গাছ।
আধঘণ্টা বাদে হঠাৎ গাড়িটার স্পিড কমে গেল। কিছু কথা না বলে হঠাৎ গাড়িটা পাশের শোল্ডারে দাঁড় করিয়ে দিল ড্রাইভার। মুখ ঘুরিয়ে তাকাল পিকুর দিকে।–পৌঁছে গেছি, নামতে পারো।
লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল পিকু। নীলচে চোখ, সোনালি আঁকড়া চুল অনেকটাই সেই চেস চ্যাম্পিয়ান ড্যানিয়েলের মতো দেখতে, মুখটা আরেকটু বেশি লম্বা। চোখের নীচটা বসা মতো।
–আমি ড্যানিয়েলের বন্ধু। বলে ডান হাতটা বিদ্যুৎবেগে বাড়িয়ে একহাতেই গলা টিপে ধরল পিকুর। দুহাত দিয়ে ওই লোহার মতো শক্ত হাত প্রাণপণে ছাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল। পিকু। কিন্তু শক্ত লোহার মতো আঙুলগুলো সাঁড়াশির মতো গলার ওপরে চেপে বসেছে। ছটফট করতে লাগল পিকু। চোখে অন্ধকার দেখতে লাগল। বুঝতে পারল মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে।
এরমধ্যে হঠাৎ কাঁচ ভাঙার শব্দ। কেউ পিকুর গলা থেকে ওই দৈত্যটার হাত টেনে সরিয়ে দিল, দৈত্যটার মুখে একটা জোরালো ঘুসি মারল। গাড়ির দরজাটা উপড়ে খুলে নিয়ে দৈত্যটাকে গাড়ি থেকে টেনে বের করে নিল।
পিকু টের পেল এখুনি আসা লোকটার সঙ্গে ট্যাক্সি ড্রাইভারের প্রচণ্ড মারামারি শুরু হয়েছে। দুজনের কেউই কম যায় না। গাড়ি থেকে কোনওরকমে হাতে ভর দিয়ে বেরিয়ে এসে খোলা বাতাসে নিশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করল পিকু। কিন্তু পারল না, ওখানেই বসে পড়ল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাল।
জ্ঞান যখন ফিরে এল মুখের সামনে চাঁদের আলোয় এক চির পরিচিত মুখ। নিজেরই মুখ। অর্থাৎ এ আর কেউ নয় ব্রায়ান। পিকুকে চোখ খুলতে দেখে ব্রায়ান বলল,এখন কেমন লাগছে? ও হল ড্যানিয়েলের বন্ধু–যার কথা বলছিলাম। এখান অবধি কীভাবে জানি ফলো করে চলে এসেছিল। নির্ঘাত এই ট্যাক্সির ড্রাইভারকে মেরে ড্রাইভার সেজে উঠে বসেছিল। ইশ, তোমার কিছু হলে ডঃ কেনকে যে কী বলতাম!
আস্তে আস্তে বাইরের পৃথিবীর মায়াবী আলো ফিরে আসছে। চাঁদটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আর তার আলোয় পিকু দেখল, ব্রায়ানের মুখটা রক্তে ভেসে যাচ্ছে, জামা রক্তে লাল হয়ে গেছে। খানিকদূরে ড্যানিয়েলের বন্ধুর দেহ পড়ে আছে।
নাক-মুখের রক্ত রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে ব্রায়ান বলে উঠল,–আমি ঠিক আছি। আর কয়েক সেকেন্ড দেরি হলে যে কী হত! চলো গাড়িতে ওঠা যাক! আর ভয় নেই। আমি আছি তো!
বলে পিকুকে পাঁজাকোলা করে তুলে গাড়ির পিছনের সিটে সস্নেহে শুইয়ে দিল ব্রায়ান। গাড়ির একদিকের দরজার পাল্লাটা না থাকায় শুতে কোনওই অসুবিধে হল না পিকুর। টের পেল ব্রায়ান গাড়ি স্টার্ট করেছে।
.
২২.
রাত দুটো। ডক্টর কেনের চোখে আজ ঘুম আসছে না। হঠাৎ সেলফোনটা বেজে উঠল। হাত বাড়িয়ে খাটের পাশে রাখা ফোনটা ধরলেন কেন।
–ডক্টর কেন, আমি ব্রায়ান বলছি।
–হ্যাঁ, বলো। তুমি পাম স্প্রিং পৌঁছে গেছো তো?
–হ্যাঁ, আমি পাম স্প্রিং-এ।
–তা এত রাতে?
–আমি পিকুকে নিয়ে আসতে পেরেছি। একটু অসুবিধে হয়েছিল।
কী?
–রজার পিকুকে আক্রমণ করেছিল। তাই রজারকে মারতে হয়েছে আমাকে।
–তাই? দীর্ঘশ্বাস পড়ল ডঃ কেন-এর। পিকু ঠিক আছে তো?
–হ্যাঁ।
–আর তুমি?
একটু যেন উৎসাহিত হল ব্রায়ান। হ্যাঁ, আমার একটু লেগেছে, মাথায় আর মুখে। ও তেমন কিছু না। স্যার, যে জন্য ফোন করেছিলাম–একটু থামল ব্রায়ান।
স্যার, আমাকে কি তৈরিই করা হয়েছে আমার ভাইকে বাঁচানোর জন্য?
–হ্যাঁ, তা হঠাৎ এরকম প্রশ্ন?
–কেন? ও তো আমার মতোই। ওর জীবন তাহলে আমার থেকে বেশি দামি কেন?
ডক্টর কেন কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। শুধু বলে উঠলেন,–শুয়ে পড়ো ব্রায়ান। কাল কথা হবে। তোমাকে আমার সঙ্গে অনেক দূর যেতে হবে।
–আর পিকু?
নাহ্, ওকে নেব না। তুমিই থাকবে আমার সঙ্গে।
ব্রায়ান ভারি খুশি হয়ে শুভরাত্রি স্যার বলে ফোনটা রেখে দিল।
.
২৩.
আজকের ভোরটা একদম অন্যরকম। সূর্য ওঠার আগেই যেন ভোর হয়ে গেছে। রাত কাটার আগেই যেন দিন শুরু। সারারাত বিছানায় শুয়ে ছটফট করছে পিকু। যন্ত্রণায় নয়, কৌতূহলে আর উত্তেজনায়। কার সঙ্গে কাল দেখা হতে চলেছে? ডঃ কেন–যার কথা ব্রায়ান একবার বলেছিল?
ডঃ কেন কি বাবার কথা জানতেন? পাম স্প্রিংস-এর মতো মরুভূমির মধ্যে এক জনহীন শহরে কী থাকতে পারে? সত্যিই কি সত্যের সন্ধান পেতে চলেছে পিকু? কুড়ি বছর আগে পিকুর জীবনের রূপ-রস-গন্ধ সবকিছু একমুহূর্তে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল যে ঘটনা, সেই ঘটনাটার পিছনে আসলে কে ছিল? সেই খারাপ লোকগুলোর সঙ্গে কি মোলাকাত হবে এবার?
এসব ভাবতে-ভাবতেই রাত শেষ হয়ে গেছে। হামাগুড়ি দিয়ে ঘরে ঢুকেছে ভোরের ক্ষীণ আলো। ব্যর্থ ঘুমটাকে ফের ডেকে না এনে সাড়ে চারটে থেকেই রেডি হয়ে রয়েছে পিকু। কথামতো ঠিক সাড়ে পাঁচটাতে ব্রায়ান এসে হাজির। পিকু হোটেলের গেটের সামনে অপেক্ষা করছিল।
গাড়িতে উঠে ব্রায়ানের দিকে তাকাল পিকু। সারা মুখে কালসিটে কাটা দাগ। ড্যানিয়েলের বন্ধু যে খুব সহজে ছেড়ে দেয়নি তার প্রমাণ ব্রায়ানের শরীরের সর্বত্র। তবু তা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে ব্রায়ান বলে উঠল,–দুর্দান্ত ঘুম হল কাল। অত পরিশ্রম হয়েছিল তো! তা তোমার রেস্ট হল কেমন? দেখে তো মনে হয় না ঘুমিয়েছ।
পিকু সায় দিল,–তা কোথায় যাচ্ছি? কার সঙ্গে দেখা করতে?
হেসে উঠে ব্রায়ান বলল,আর তো মিনিট দশেকের অপেক্ষা। তারপর সব প্রশ্নের জবাব পাবে।
তুমি ডাক্তার দেখিয়েছ? কাল আমার জন্য যা করলে!
হেসে উঠল ব্রায়ান। খুব সহজভাবে বলল,আমার জন্ম-মৃত্যু সবই তো তোমার জন্য তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। বলে পিকুর দিকে তাকাল। ব্রায়ানের গভীর দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে পিকু বুঝল যে ও কথাটা হালকাভাবে বলছে না।
মিনিট দশেক পরে ওদের গাড়ি একটা একতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বিল্ডিংটার ওপরে লেখা ম্যাভেরিক ফ্লাইং ক্লাব।
গাড়িটা পার্কিং-এ রাখার সময় পিকু দেখল বাড়িটার পেছনে বড় হেলিপ্যাড। বেশ কয়েকটা হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। ওরা বাড়ির মধ্যে না ঢুকে পাশের রাস্তা দিয়ে। সরাসরি হেলিপ্যাডে চলে এল। বাড়িটার পিছন দিকে হেলিপ্যাডের আগেই একটা গোল টেবিল পাতা। তাতে তিনটে চেয়ার। একটা চেয়ারে অন্যদিকে মুখ করে একজন বসে আছে। বড় গোল টেবিলটার ওপরে একটা কাঠের বাক্স রাখা।
–ডঃ কেন, আমরা এসে গেছি। ব্রায়ান দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল টেবিলটার দিকে।
পিকুও দ্রুত পায়ে ব্রায়ানের পিছু পিছু হাঁটছিল, কিন্তু হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মনে হল, পরিচিত গলায় ডঃ কেন যেন মৃদুস্বরে গাইছেন, সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে। ভ্ৰমিছ দীনপ্রাণে সতত হায় ভাবনা শতশত, নিয়ত ভীতপীড়িত…
ব্রায়ান ফের বলল,ডঃ কেন, আমি আর পিকু এসে গেছি। গান থামিয়ে ডঃ কেনও ঘুরে দাঁড়িয়েছেন।
–বাবাই। পিকু চিৎকার করে উঠল। ছুটে এগিয়ে গেল ডঃ কেনের দিকে। তারপর। দাঁড়িয়ে পড়ল। অভিমানে চোখ ফেটে জল আসছে। এতদিন বাবাই ওকে ছেড়ে থাকতে পেরেছে। যাকে গত কুড়িবছর ধরে প্রতি মুহূর্তে পিকু খুঁজেছে, সে খোঁজা অর্থহীন জেনেও–সেই বাবাই সশরীরে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে? এত নিরুত্তাপ হয়ে?
কান্না আর থামিয়ে রাখতে পারল না পিকু। সে কান্না আনন্দের, না দুঃখের, না অভিমানের কে জানে? জয়ন্ত এগিয়ে এসে বুকে জড়িয়ে ধরল পিকুকে। জয়ন্তর চোখেও জল। খানিকবাদে ধরা গলায় বলে উঠল,–কেমন আছিস রে অদ্ভুত! অনেক বড় হয়ে গেছিস।
পিকু ছোটবেলায় ভূতের নামে খুব ভয় পেত বলে, ওকে মজা করে জয়ন্ত মাঝেমধ্যে অদ্ভুত বলে ডাকত। বলত ওই নাম শুনলে, ভূতেরা পালায়।
চেয়ারে বসে জয়ন্ত বলল,আমার উপায় ছিল না রে! আমেরিকার সরকার ওদের প্রোজেক্টে আমার সাহায্য পেতে আমার বিরুদ্ধে টেররিজমের চার্জ এনেছিল। যাতে আমি ওদের সাহায্য করতে বাধ্য হই। রিপোর্টে প্রকাশ না করলেও প্লেনে বিস্ফোরণের জন্য আমাকেই দায়ী করেছিল। তা ছাড়া আমিও তো ছিলাম ওই তিরিশজন যাত্রীর একজন। তাই প্লেনে না উঠেও চিরকালের মতো হারিয়ে গেল জয়ন্ত। আমাকে নিয়ে আসা হল এখানে যেখান থেকে কারুর পক্ষেই আর বেরোনো সম্ভব নয়।
পিকু অভিমানী গলায় বলে উঠল, মা মারা গেছে দু-বছর আগে। আমার মতো মার জীবনও শেষ হয়ে গিয়েছিল তোমার হঠাৎ চলে যাওয়ায়।
জয়ন্ত চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। তারপর বলল, আমার পক্ষে কিছু জানা সম্ভব ছিল না। যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে তোরাও রেহাই পেতিস না। তাও যে একেবারে চেষ্টা করিনি তা নয়। খুব মন খারাপ লাগলে তোদের বাড়িতে ফোন করে রিং হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে কেটে দিতাম। ওরা বলেই রেখেছিল কোনওভাবে তোরা খবরটা পেলে তোদেরকে মারতে ওরা একমুহূর্তও দ্বিধা করবে না। গত কুড়ি বছর আমার এখানেই কেটেছে প্রোজেক্ট এইচ-এ। দুদিন আগেই প্রোজেক্ট এইচ বন্ধ হয়ে গেছে। তবে আমাকে ওরা আজও ছাড়বে না, সব খবর তাহলে বাইরে চলে যাবে।
পিকু বাবাই-এর মুখের দিকে তাকাল। চুল সব পেকে গেছে। মুখে বয়সের সামান্য ছাপ পড়লেও চোখের সেই দীপ্তি, মুখের স্মিত হাসি এতটুকুও ম্লান হয়নি।
বাবার হাতটা চেপে ধরল পিকু,–এবার তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবই বাবাই। পেয়েছি যখন সারা পৃথিবীর সঙ্গে লড়তে হলেও লড়ব। কিন্তু তোমাকে কোনওভাবেই ছাড়ব না। সেরকম হলে আমিও এখানেই থেকে যাব। ওখানেই বা আমার কে আছে?
জয়ন্ত হেসে উঠল। বুঝতে পারল ছোটবেলার সেই জেদ-বায়না আজও পিকুর মধ্যে একইভাবে রয়ে গেছে।
জয়ন্ত বলল,আমাকে যে আবার একটা জরুরি কাজে ফিরতে হবে সোনা, সেখানে শুধু একজনই আমার সঙ্গে যেতে পারবে, তা কাকে নেব? তোকে না ব্রায়ানকে?
–আমাকে বাবাই! জোরে চিৎকার করে উঠল পিকু। পাশে দাঁড়িয়ে পিকুর ছেলেমানুষি দেখে মিটিমিটি হাসছে ব্রায়ান।
জয়ন্ত বলে উঠল, ব্রায়ান তোর ভাই। সেটা করলে ওর প্রতি অন্যায় হয়ে যাবে।
তাহলে আমরা দুজনেই যাব।
না, তা তো হয় না। বললাম না। একজনই শুধু সঙ্গে যেতে পারবে। তার থেকে। আমরা অন্যভাবে ডিসাইড করব। তোদের দুজনের মধ্যে চেস হোক তাহলে। যে জিতবে, সে যাবে।
পিকু খুব উৎসাহিত হয়ে লাফিয়ে উঠল, হ্যাঁ, চেস। চেসেই তাহলে ঠিক হবে।
জয়ন্ত হেসে উঠল, তুই আমার মতোই হয়েছিস বটে। ছেলেমানুষি আর গেল না। খেল, তবে শুধু এটা বলে রাখি–তুই যার কাছে হেরেছিস সেই ড্যানিয়েলকে ব্রায়ান প্রত্যেকবার। হেসে খেলে হারায়। তারপরেও?
একটু চিন্তায় পড়ে গেল পিকু,–তাহলে দৌড়? আমি দৌড়ে খুব ভালো।
ফের হেসে উঠল জয়ন্ত,–পাগল হয়েছিস? ব্রায়ান ঠিক তোর মতো হলেও ও সুপারহিউম্যান। ওকে আমি চিতাবাঘের স্পিড় দিয়েছি আর বাঘের শক্তি দিয়েছি–যাতে তোর বিপদে ও কাজে লাগে। তুই পারবি ওর সঙ্গে?
পিকু কাঁদো কাঁদো গলায় এবার বলে উঠল, কিন্তু আমি যাবই। বলো কী করলে পারব? অসহায় ভাবে ব্রায়ানের দিকে আড়চোখে তাকাল পিকু। ব্রায়ান এখনও মুচকি মুচকি হাসছে।
লুডো! লুডো খেলবি? পিওর লাক। যে জিতবে সেই সঙ্গে যাবে আমার। বোর্ডও আছে সঙ্গে। বলে টেবিলের ওপরে রাখা বাক্সটা খুলে ফেলল জয়ন্ত। বড় লুডোর বোর্ড। পুরোটা ডিজিটাল। কিন্তু ছক্কা নেই। দুদিকে ডিজিটাল প্যানেল, তাতে দুদিকে বাটন।
জয়ন্ত পিকুকে বলল,–এই বাটন প্রেস করলে, 1 থেকে 6 যে-কোনও একটা নাম্বার পড়বে। একবার তুই, একবার ব্রায়ান। যেরকম নাম্বার পড়বে, ঠিক সেরকমভাবে খুঁটি আপনা থেকে বোর্ডের ওপর সরে যাবে। ধর তোর 3 পড়ল, তুই আছিস 42-এ, আপনা থেকে ঘুঁটি 45-এ চলে যাবে। তারপর সিঁড়ি বা সাপ–যেরকম থাকবে ওই ঘরে, সেই অনুযায়ী ঘুঁটি সেখানে। চলে যাবে। কিন্তু হেরে গেলে কোনওরকম বায়না করা চলবে না–ঠিক তো?
পিকু ঘাড় নেড়ে সায় দিল। এ ছাড়া ওর আর কোনও আশাই নেই। ব্রায়ান লাল গুটি নিল। পিকু সবুজ। বরাবরই পিকু সবুজ নিত। খানিকক্ষণের মধ্যেই পিকুর ঘুটি লাফিয়ে লাফিয়ে 90-এর ঘরে উঠে গেল। কিন্তু, তার পরেই 96-এ সাপের মুখে পড়ে একেবারে 17। ব্রায়ানকেও দু-তিনবার সাপে খেল। পিকুকে আরেকবার 98-এর সাপ খেয়ে সোজা পাঠিয়ে দিল 57-এ।
জয়ন্ত পাশে বসে শুধু মুচকি মুচকি হাসছে। আর ওদের ছেলেমানুষি লড়াই দেখছে। প্রোজেক্ট এইচ-এর পরিত্যক্ত হেলিপ্যাডে লড়াই চলেছে দুই ছেলের মধ্যে। ব্রায়ানের মধ্যে কোনও উত্তেজনা নেই। পিকুই মাঝে মাঝে নখ কামড়াচ্ছে। চাল দেওয়ার আগে পায়চারি করে এসে অনির্দিষ্ট কাউকে লক্ষ্য করে কপালে হাত ঠুকে প্রণাম জানিয়ে চাল দিচ্ছে। মাঝে মাঝে সিঁড়ি পেলে লাফিয়ে উঠছে। সাপের মুখে পড়লে রেগে চেঁচিয়ে উঠছে। এটা আজ ওর জীবনমরণের লড়াই। জীবন ফিরে পাওয়ার লড়াই।
কিন্তু আজও ভাগ্য পিকুর সঙ্গে নেই। শেষে ব্রায়ানই জিতে গেল। পিকু মুখ ঢেকে কাঁদতে শুরু করল। জয়ন্ত উঠে পিকুকে জড়িয়ে ধরল।
–তুই সত্যিই বড় হোসনি। আরে, সবসময় আমি তোর সঙ্গে থাকব। যেমন ছিলাম। কাছে থাকলেই কি শুধু থাকা হয়? আর ছোঁয়া না গেলেই কি তাকে দেখা যায় না? ওই ওপরের দিকে তাকা। নীল আকাশ–কোনওদিন ছুঁয়ে দেখতে পারবি? কিন্তু সবসময় সঙ্গে থাকে। আমিও সেরকম।
–আসি পিকু। ভালো থাকিস। জড়িয়ে ধরে আবার ছোট বাচ্চার মতো আদর করে পিকুকে জয়ন্ত। ব্রায়ানও এসে জড়িয়ে ধরে পিকুকে। পিঠ চাপড়ে বলে ওঠে, বেটার লাক নেক্সট টাইম। বাবা কিন্তু আমাকেই তোমার থেকে বেশি ভালোবাসেন।
জয়ন্ত আর ব্রায়ান একটা হেলিকপ্টারের দিকে এগিয়ে যায়। ব্রায়ান পাইলটের আসনে বসে। জয়ন্ত অন্য দরজা দিয়ে উঠতে গিয়ে ফের ফিরে আসে। আবার আদর করে জড়িয়ে ধরে। তারপর পিকুর হাতে একটা খাম দিয়ে বলে,–এটা পরে পড়ে দেখিস। মন খারাপ করিস না।
জয়ন্ত ফিরে গিয়ে অন্য দরজা দিয়ে হেলিকপ্টারে ওঠে। ওপরের রোটর ব্লেড চালু হয়েছে হেলিকপ্টারের, মাতালের মতো একটু এদিক-ওদিক করে মাটি ছেড়ে সোজাসুজি বারো তেরো ফুট উঠে গেল হেলিকপ্টারটা। তারপর ছুটে চলল সামনের দিকে। প্রায় আধকিলোমিটার মতো সোজা গিয়ে বাঁক নিয়ে ওপরের দিকে উঠল হেলিকপ্টার। তখনই একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। আগুনে জ্বলতে জ্বলতে হেলিকপ্টারটা নীচের দিকে নেমে এল।
পিকু পাগলের মতো দৌড়োতে শুরু করল হেলিকপ্টারের দিকে। মাঝে যেন কোনও পথ নেই। পিকুর পুরো দুনিয়াটা আবার দুলিয়ে দিয়ে আরেকবার ওই দিক থেকেই বিস্ফোরণের আওয়াজ এল। হেলিকপ্টারের ছোট ছোট টুকরো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।
বেশ খানিকটা ছুটে হঠাৎ করে বসে পড়ল পিকু। নাহ্, এ ছোটার আর কোনও অর্থ নেই। ওরকম বিস্ফোরণের পরে ওদের কোনওই চিহ্ন থাকবে না।
.
২৪.
দুদিন বাদে সুবীর রায়ের বাড়িতে খামটা খুলেছিল পিকু। ছোট চিঠি।
পিকু, এ চিঠি যখন পড়বি তখন আমি অনেক দূরে চলে গেছি, ব্রায়ানকে সঙ্গে নিয়ে। এ পৃথিবীটা থাকুক সাধারণ মানুষদের জন্য। তাই ব্রায়ানকে সঙ্গে নিয়েই গেলাম। শেষ অতিমানব। আমাকে তো এমনিতে মরতেই হত। এই প্রথমবার লুডোয় তোকে ঠকালাম। এমনভাবে প্রোগ্রাম করা ছিল যে লাল ঘুটি ছাড়া অন্য যে-কোনও ঘুটি নিলেই হারতিস। সেভাবেই সংখ্যাগুলো আসছিল। র্যানডমলি নয়। কি, বোকা বানিয়েছি তো!
থাকগে, আসল কথায় আসি। আমি তো মরতে চাইনি পিকু। তোদের সবাইকে নিয়ে বাঁচতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু কি যে হল! হঠাৎ করে একদিন বুঝলাম আমার জীবন আর আমার হাতে নেই। কে যেন হঠাৎ করে আমার সবকিছু কেড়ে নিয়ে আমাকে এক ছোট্ট খাঁচায় বন্দি করে ফেলেছে। সেখানে ভোরের আলো নেই, রাতে তারাজ্বলা আকাশ নেই, সামনে লুডোর বোর্ড নেই, সঙ্গে তোরা নেই। আমি একা। বড় একা।
মন খারাপ করিস না, আমি সবসময় তোর সঙ্গে ছিলাম, থাকবও। আমরা চাঁদের আলোয়, তারার হাসিতে মনে মনে কথা বলব। তোর জন্য একটা ছোট কবিতাও লিখলাম। ছোটবেলায় আমার কবিতা শুনলেই খেপে গিয়ে খিমচে দিতিস। আজ তো সে উপায় নেই। শোনাবই– এ আমারই জীবনের কথাযার সবটুকু জুড়ে তুই।
বন্ধ খামের এপিঠে-ওপিঠে লিখে যাই কিছু কথা।
খামের ভেতরে স্মৃতি হয়ে থাক কিছু প্রিয় নীরবতা।
(গল্পে উল্লিখিত সব চরিত্র কাল্পনিক)