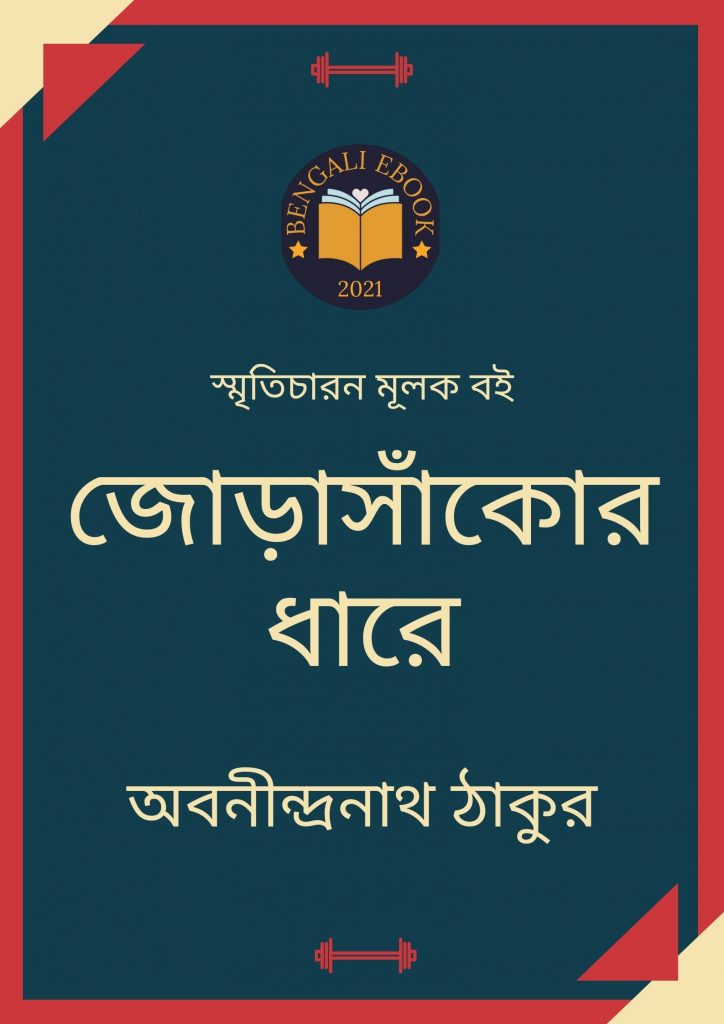- বইয়ের নামঃ জোড়াসাঁকোর ধারে
- লেখকের নামঃ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
- প্রকাশনাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
- বিভাগসমূহঃ গল্পের বই
০১. বর্ষামঙ্গল
ভূমিকা
যত সুখের স্মৃতি এত দুঃখের স্মৃতি আমার মনের এই দুই তারে যা দিয়ে দিয়ে এইসব কথা আমার শ্রুতিধরই শ্রীমতী রানী চন্দ এই লেখায় ধরে নিয়েছেন, সুতরাং এর জন্যে যা কিছু পাওনা তাঁরই প্রাপ্য।
মুখের কথা লেখার টানে ধরে রাখা সহজ নয়, প্রায় বাতাসে ফাঁদ পাতার মতও কঠিন ব্যাপার সুতরাং যদি কিছু দোষ থাকে এই বইখানিতে সেটা আমি নিতে রাজি হলেম ইতি
শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
জন্মাষ্টমী
১৩৫১
————–
১
তোমাদের এখানে আজ বর্ষামঙ্গল হবে? আমাদেরও ছেলেবেলা বর্ষামঙ্গল হত। আমরা কি করতুম জানো? আমরা বর্ষাকালে রথের সময়ে তালপাতার ভেঁপু কিনে বাজাতুম; আর টিনের রথে মাটির জগন্নাথ চাপিয়ে টানতুম, রথের চাকা শব্দ দিত ঝন্ ঝন্; যেন সেতার নূপুর সব একসঙ্গে বাজছে। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ত দেখতে পেতুম, থেকে থেকে মেঘলা আলোকে রোদ পরাত চাপাই শাড়ি—কি বাহার খুলত! তবে শোনো বলি একটা বাদলার কথা। সন্ধ্যে হতে ঝড়জল আরম্ভ হল, সে কি জল, কি ঝড়! হাওয়ার ঠেলায় জোড়াসাঁকোর তেতালা বাড়ি যেন কাঁপছে, পাকা ছাত ফুটো হয়ে জল পড়ছে সব শোবার ঘরে। পিদিম জ্বালায় দাসীরা, নিবে নিবে যায় বাতাসের জোরে। বিছানাপত্তর গুটিয়ে নিয়ে দাসীরা আমাদের কোলে করে দোতলায় নাচঘরে এনে শোয়ালে। বাবা মা, পিসি পিসে, চাকর দাসী, ছেলেপুলে, সব এক ঘরে। এক কোণে আমাকে নিয়ে আমার পদ্ম দাসী কটর কটর কলাই ভাজা চিবোচ্ছে, আমাকেও দু-একটা দিচ্ছে আর ঘুম পাড়াচ্ছে, চুপি চুপি ছড়া কাটছে—ঘুমতা ঘুমায়; গাল চাপড়াচ্ছে আমার, পা নাচাচ্ছে নিজের ছড়া কাটার তালে তালে।
ওদিকে শোঁ-শোঁ শব্দ করছে বাইরের বাতাস; এক-একবার নড়েচড়ে উঠছে বড় ঘরের বড় বড় কাঠের দরজাগুলো। খানিক ঘুমিয়ে খানিক জেগে কাটল ঝড়ের রাত। সকালে কাক পাখি ডাকে না, আকাশ ফরশা হয় না। মাছের বাজারে মাছ আসেনি, পানবারুই পান আনেনি। শশী পরামানিক এসে খবর দেয়, শহরের রাস্তায় হয়েছে এককোমর জল।
ও দিব্য ঠাকুর, আজ কি রান্না?—‘ভাতে ভাত খিচুড়ি’ বলে খুন্তি হাতে চলে যায় রান্নাবাড়ির দিকে। কেরঞ্চি গাড়ি? গাড়ি চলল না আপিসের দিকে, গোরুর গাড়িতে ব্যাঙের ছাতার নিচে বসে ব্যাঙ্কের বড়বাবুরা সরকারি কাজে যাচ্ছেন। সিংগিদের পুকুর ভেসে মাছ পালিয়েছে। পাড়ার লোক ধরে ধরে ভেজে খাচ্ছে। হিরু মেথর এসে খবর দিতেই, বেরিয়ে পড়ল বিপনে চাকর ছোট ডিঙি বেয়ে শহরের অলিগলিতে ফিরতে। কাগজের নৌকো চলল আমাদের ভেসে—এ গাছ ঘুরে, ও বাগানে ডুবে-যাওয়া গোল চক্কর ঘুরে, একটানা স্রোতে পড়ে-চলতে চলতে, ফটকের লোহার শিকে ঠেকে উলটে পড়ল কাদায় জলে লট্পট্ একগোছা বিচিলির লঙর ফেলে।
ঈশ্বর দাদা খোঁড়াতে খোঁড়াতে লাঠি ঠকঠকিয়ে ভিস্তিখানায় এসে হাঁকলেন ‘বিশ্বেশ্বর!’ যাই—বলে বিশ্বেশ্বর হুঁকো কল্কে হাতে দিতেই—“শনি সাত, মঙ্গলে তিন, আর সব দিন দিন’ বলতেই হুঁকো শব্দ দিতে থাকল—চুপ চুপ—ছুপ ছুপ —কুর্র্—ঝুপ ঝুপ। তখন বর্ষাকাল পড়লে সত্যি সত্যি বৃষ্টি ঝড় আকাশ ভেঙে খড়ের চাল খোলার চাল ফুটাে করে আসত। এ দেখেছি। ডালে চালে খিচুড়ি চেপে যেত। মেঘ করলেই শহর বাজার ডুবত জলে, পুকুরের মাছ উঠে আসত রান্নাবাড়ির উঠানে খেলা করতে করতে—ধরা পড়ে ভাজা হয়ে যেত কখন বুঝতেই পারত না।
ফুটে ছাত—ভাতে ভাত
ভাজ্ মাছ।
সারারাত সাতদিন ঝমাঝম্। মটর ভাজি কড়াই ভাজি ভিজে ছাতি। যেদিকে চাও ভিজে শাড়ি ভিজে কাপড় পরদা টেনে হাওয়ায় দুলছে, তারই তলায় তলায় খেলে বেড়ানো সারাদিন, সন্ধ্যে থেকে কোলা ব্যাঙে বাদ্যি বাজায়, রাজ্যের মশা ঘরে সেঁধোয় টাকাংদিং টাকাংদিং মশারি ঘিরে। দাসী চাকর সরকার বরকার সবার মাথায় চড়ে গোলপাতার ছাতা; শোলার টুপি, ওয়াটারপ্রুভ, রেনকোট ছিল না; ছিল ছেলেবুড়ো মিলে গান গল্প, বাবু ভায়ে মিলে খোস গল্প—আর কত কি মজা আঠারো ভাজা জিবেগজা। গুড়গুড়ি ফরসী দাদুরীর বোল ধরত গুড়ুক ভুড়ুক।
০২. ছোট ছেলেরা হো-হো করে স্কুলে যায়
এখানে দেখি ছোট ছেলেরা হো-হো করে স্কুলে যায়, আসন খাতা বই দু-হাতে বুকে জড়িয়ে নিয়ে। কত ফুর্তি তাদের, এমন স্কুল আমার ছেলেবেলায় পেলে আমিও বুঝিবা একটু আধটু লেখাপড়া শিখলেও শিখতে পারতুম। বাড়ির কাছেই নর্ম্যাল স্কুল; কিন্তু হলে হবে কি? নিজের ইচ্ছেয় কোনোদিন যাইনি স্কুলে। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াই, আজ পেটে ব্যথা, কাল মাথাধরার ছুতো— রেহাই নেই কিছুতেই। স্কুলে যাবার জন্য গাড়ি আসে গেটে। চিৎকার কান্নাকাটি—যাব না, কিছুতেই যাব না। চাকররা জোর করে গাড়িতে তুলবেই তুলবে। মনে হয় গাড়ির চাকা দুটো বুকের উপর দিকে চলে যাক্—সেও ভালো, তবু স্কুলে যাব না। মহা ধ্বস্তাধস্তি, অতটুকু ছেলে পারব কেন তাদের সঙ্গে? আমার কান্নায় ছোটপিসিমার এক-একদিন দয়া হয়, বলেন ‘ও গুনু, নাইবা গেল অবা আজ স্কুলে। রামলালকে বলেন, ‘রামলাল, আজ আর ও স্কুলে যাবে না, ছেড়ে দে ওকে।’ কোনো কোনো দিন তার কথায় ছাড়া পাই। কিন্তু বেশির ভাগ দিনই চাকররা আমায় দু-হাতে ধরে ঠেলে গাড়ির ভিতরে তুলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। গাড়ি চলতে শুরু করে, কি আর করি, জোরে না পেরে বন্দী অবস্থায় দু-চোখের জল মুছে গুম হয়ে বসে থাকি। স্কুল ভালো লাগে না মোটেই। ভালো লাগে শুধু স্কুলে একটি ঘরে কাচের আলমারিতে তোলা একখানি খেলনার জাহাজ আর গোটাকয়েক নানা আকারের শঙ্খ—। বেশির ভাগ সময় কাচের আলমারির সামনে বসে বসে সেগুলো দেখি। জানো, আমার ছবি আঁকার হাতেখড়ি হয় সেইখানেই, ওই নর্ম্যাল স্কুলেই। আর কোনো বিদ্যের হাতেখড়ি তো হল না, তবু ভাগ্যিস ওই হাতেখড়িটুকু হয়েছিল। তাই না তোমাদের এখনও একটু ছবি-টবি এঁকে দিয়ে খুশি রাখতে পারি। নয়তো আর কারে কোনো কাজেই লাগতুম না আমি। এখন শোনো তবে সেই হাতেখড়ির গল্প।
একটি মেটে কুঁজো, একটি মেটে গ্লাস, ছবির হাতেখড়ি আমার এই দুটি দিয়ে। বললুম তো, আমি তখন নর্মাল স্কুলে, পড়াশুনা করি বলব না, যাওয়া-আসা করি। পাশেই বড় ছেলেদের ক্লাস, সেই ক্লাসের জানালার ধারে গিয়ে সময় সময় বসে থাকি। বোতল বোতল ভরা লাল নীল জল নিয়ে মাস্টারমশায় ঢালাঢালি করেন; লাল হয় নীল, নীল হয় লাল, মাঝে মাঝে লাল নীল দুইই উবে যায়, বোতলে পড়ে থাকে ফিকে রঙের জল খানিকটে, চেয়ে চেয়ে দেখি, ভারি মজা লাগে। কেমিয়াবিদ্যা শেখানো হয়ে গেলে আসেন সাতকড়িবাবু ড্রইং মাস্টার। একটা মোট কাগজে বড় বড় করে আঁকা একটি মেটে কুঁজো ও গ্লাস, সেইটে কালো বোর্ডের গায়ে ঝুলিয়ে দিয়ে ছেলেদের বলেন, ‘দেখে দেখে আঁকো এবারে।’ ছেলেরা তাই আঁকে খাতার পাতায়। মাস্টার ঘুরে ঘুরে সবার কাছে গিয়ে দেখেন। এখন সেই ক্লাসে আছে আমাদের পাশের গলির ভুলু। একসঙ্গেই স্কুলে যাওয়া-আসা করি। তাকে ধরে পড়লুম, ‘কি করে কুঁজো আর গ্লাস আঁকতে হয় আমায় শিখিয়ে দে, ভাই।’ তার কাছে কুঁজো গ্লাস আঁকা শিখে ভারি ফুর্তি আমার। যখন-তখন সুবিধে পেলেই কুঁজো গ্লাস আঁকি। বড় মজা লাগে, কুঁজোর মুখের গোল রেখাটি যখন টানি। মন একেবারে কুঁজোর ভিতরে কুয়োর তলায় ব্যাঙের মতে টুপ করে ডুব দিতে চায়। আর সেই কাচের আলমারির স্টীম জাহাজ—তাতে চড়ে বসে মন কাপ্তেন হয়ে যেতে চায় সাত সমুদ্দর তেরো নদীর পার। কি খেলার জাহাজই ছিল সেটি—পালমাস্তুল, দড়িদড়া, যেখানকার যা হুবহু আসল জাহাজের মতো।
ভুলু আমায় প্রায়ই বলে, ‘ভালো করে লেখাপড়া কর্—দেখবি এই জাহাজটিই তুই প্রাইজ পেয়ে যাবি। কিন্তু লেখাপড়ায়ই যে মন বসে না আমার, তা প্রাইজ পাবো কোত্থেকে? কোনো আশা নেই জানি, তবুও লোভ হয় মনে এক-আধটা প্রাইজ পেতে। কিন্তু কোনোবার কোনো কিছুরই জন্য প্রাইজ আর পেলেম না নর্ম্যাল স্কুলে।
একবার প্রাইজ বিতরণের সময় এল, ইস্কুলে ছিল একটা মস্ত বড় ঘর আগাগোড়া গ্যালারি সাজানো। এক পাশে আছে খানকয়েক চেয়ার ও একটা টেবিল। রোজ ক্লাস আরম্ভ হবার আগে ছোট বড় সব ছেলেরা সেই ঘরে জড়ো হই। রেজিস্টার খুলে মাস্টার একে একে নাম হাঁকেন; আমরা বলি, ‘প্রেজেন্ট স্যার, অ্যাবসেন্ট স্যার।’ নাম ডাকা সারা হলে শুরু হয় ড্রিল। গ্যালারিতে বসে ছিলুম, উঠে দাঁড়াই এবার। মাস্টার হেঁকে চলেন, ‘দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন, বাম হস্ত উত্তোলন, অঙ্গুলি সঞ্চালন। অমনি আমাদের পাঁচ পাঁচ দশটা অঙ্গুলি থর থর করে কাঁপতে থাকে যেন কচি কচি আমপাতা নড়ছে হাওয়াতে। তারপর পদক্ষেপ; ডান পা বাঁ পা তুলে বেঞ্চিতে খুব খানিকটে ধুপ ধাপ ঠুকে যার যার ক্লাসে যাই।
সেই বড় ঘর সাজানো হয়েছে প্রাইজ বিতরণের দিনে, টেবিলের উপরে লাল ফিতেয় বাঁধা গাদা গাদা চটি মোটা সোনালি রুপোলি নানা রঙের বই। সামনে এক সারি চেয়ার—বিশিষ্ট লোকেরা বসবেন তাতে। আমরাও সকলে হাজির গ্যালারিতে অনেক আগে থেকেই। প্রাইজ বিতরণের আগে জিতেন বাঁড়ুজ্জে কুস্তি দেখালেন—লোহার শিকল ছিঁড়লেন, লোহার বড় বড় বল ছুঁড়ে ছুঁড়ে লুফে নিলেন। মস্ত পালোয়ান তিনি।
এবার প্রাইজ বিতরণ হবে। গোপালবাবু হেডমাস্টার, টাকমাথা, ঘাড়ের কাছে একটু একটু চুল, অনেকটা এই এখনকার আমার মতোই; তবে রঙ তাঁর আরো পরিষ্কার। গম্ভীর মানুষ; কামিয়ে জুমিয়ে ফিটফাট হয়ে গলায় চাদর ঝুলিয়ে এসে বসলেন চেয়ারে। ছেলেরা কেউ বুঝুক ন-বুঝুক এই সব উপলক্ষে তিনি ইংরেজিতেই বক্তৃতা করেন। তিনি তাঁর লম্বা ইংরেজি বক্তৃতা শেষ করলেন। তারপর এইবারে একজন মাস্টার উঠে যারা প্রাইজ পাবে তাদের নাম পড়ে যেতে লাগলেন। ছেলেদের নাম ডাকা হতেই তারা টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, হেডমাস্টার মশায় তাদের হাতে লাল ফিতেয় বাঁধা প্রাইজ তুলে দেন। এক-একটি প্রাইজ দেওয়া হয় আর আমরা হাততালি দিয়ে উঠি, যে যত জোরে পারি। হাততালির ধুম কি। লাল হয়ে উঠল হাতের তেলো, তবু থামিনে। সেবার অনেকেই প্রাইজ পেলে; তার মধ্যে ভুলু পেলে, সমরদাও একটা পেয়ে গেলেন for good conduct, চেয়ে চেয়ে দেখি আর ভাবি এইবার বুঝি আমার নাম ডাকবে, আমাকে এমনি একটা কিছুর জন্য হয়তে প্রাইজ দিয়ে দেবে। কান পেতে আছি নাম শোনবার জন্য; শেষ প্রাইজটি পর্যন্ত দেওয়া হয়ে গেল, কিন্তু আমার কানে আমার নাম আর পৌঁছল না। প্রাইজ বিতরণ হয়ে গেলে মাস্টার উঠে পড়লেন, ছেলেরা হৈ হৈ করে বাইরে এল ; আর আমি তখন দু-চোখের জলে ভাসছি। ভুলু সাত্ত্বনা দেয়, ‘আরে, তাতে কি হয়েছে, ভাল করে পড়াশুনো কর্, সামনের বারে ভালো প্রাইজ ঠিক পাবি তুই।’ সে কথায় কি মন ভোলে? না-পাওয়া মণ্ডার জন্য বাচ্চু বেজিটা যেমন হয়ে থাকে আমারও মনটার তেমনি দশা হয়। চোখের ধারা গড়াইতেই থাকে, থামে না আর। শেষে ভুলু বললে, ‘প্রাইজ চাস তুই, এই কথা তো? আচ্ছা এই নে’—বলে খাতা থেকে একটুকরো সাদা কাগজ ছিঁড়ে তাতে খসখস করে কি সব লিখে আমার হাতে দিলে। আমি তাতেই খুশি। কাগজের টুকরোটি যত্নে ভাঁজ করে পকেটে রেখে চোখের জল মুছে বাড়ি এলেম। বৈঠকখানায় বাবামশায় পিসেমশায় সবাই বসে ছিলেন। বললেন, ‘দেখি কে কি প্রাইজ পেলি।’ সমরদা তাঁর প্রাইজ লালফিতে-বাঁধা টিকিট-মারা সোনালি বই দেখালেন। আমি বললুম, ‘আমিও পেয়েছি।’ পিসেমশায় বললেন, ‘কই দেখি?’ গম্ভীরভাবে পকেট থেকে ভাঁজকরা সাদা কাগজটুকু বের করে তাঁদের সামনে মেলে ধরলুম। উলটেপালটে সেটি দেখে তাঁরা হো-হো করে হেসে উঠলেন। তখন বুঝলুম, ভুলুটা আমায় ঠকিয়েছে। এমন রাগ হল তার উপরে! রাত্তিরে খাওয়াদাওয়া সেরে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লুম। সকালে ঘুম ভেঙে দেখি প্রাইজ না-পাওয়ার দুঃখু আর একটুও নেই।
তা লেখাপড়ায় মন বসবে কি? তোমাদের মতো তো গাছের ছায়ায় খোলা হাওয়ায় বসে পড়তে পাইনি কখনও। স্কুলের ওই পাকা দেয়াল-ঘেরা বন্ধ ঘরের ভিতরে দম যেন আটকে আসে আমার। যতক্ষণ পারি ঘরের বাইরেই ঘোরাফেরা করি। স্কুলের পাশে শ্যাম মল্লিকের বাড়ি, তাদের বাড়ির একটি মেয়ে পড়তে আসে আমাদের স্কুলে, ইজের চাপকান প’রে, বেণী ঝুলিয়ে। তাদের বাড়িতে একটা পোষা কালো ভাল্লুক চরে বেড়ায় সামনের বাগানে, দেখা যায়, ইস্কুল থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাল্লুক দেখি। ইস্কুলঘরের বাইরে যা কিছু সবই আমার কাছে ভালো লাগে। ইস্কুলের গেটের কাছে রাস্তা। নানা রকম লোক যাচ্ছে আসছে, তাদের আনাগোনা দেখি। এই রকম দেখতে দেখতে একদিন যা কাণ্ড। কাবুলিওয়ালার রাগ দেখেছ কখনও? গেটের কাছে কতগুলি কাবুলিওয়ালা রোজই বসে থাকে আঙুর বেদানা নিয়ে। টিফিনের সময়ে ছেলেরা কিনে খায়। সেদিন হয়েছে কি, বড়ছেলেদের মধ্যে কে একজন বুঝি এক কাবুলিকে বলেছে ‘বেইমান’। আর যায় কোথায়! দেখতে দেখতে সব কয়টা কাবুলি উঠল রুখে, দারোয়ান বুদ্ধি করে তাড়াতাড়ি লোহার ফটকটা দিলে বন্ধ করে। বাইরে কাবুলি, ভিতরে ছেলের দল; রাস্তা থেকে পড়তে লাগল টপাটপ কাবলাই বেদানা। মাথার উপরে যেন এক চোট শিলাবৃষ্টি হয়ে গেল। জানো তো, মারপিট দেখলে আমি থাকি বরাবরই সবার পিছনে। শিশুবোধে চাণক্যশ্লোক মনে পড়ে—ন গণস্যাগ্রতো গচ্ছেৎ। তা, বাপু, সত্যি কথাই বলব। আমি ওই পিছনে থেকেই ফাটা বেদানাগুলো ফাঁকতালে কুড়িয়ে কুড়িয়ে খেতে লাগলুম। সেদিনের ঝগড়ায় জিত হল বটে আমারই। কিন্তু ইস্কুলের ছুটির পর বাড়ি ফিরতে হবে; কাবুলিওয়ালার ভয় যায় না। পালকির ভিতরে বসে আচ্ছা করে দরজা বন্ধ করে অতি ভয়ে ভয়ে বাড়ি ফিরি শেষে।
নর্ম্যাল স্কুলের এক-এক পণ্ডিতের চেহারা যদি দেখতে তো বুঝতে কেমন পণ্ডিত সব ছিলেন তারা। আমাদের পড়ান লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত, চেহারা তাঁর ঠিক যেন মা দুর্গার অসুর। মস্ত বড় মাথা, কালো কুচকুচে গায়ের রং, বোয়াল মাছের মতো চোখ দুটাে লাল টকটক করছে। তাঁর কাছে পড়ব কি? যতক্ষণ ক্লাসে থাকি শিশুমন কাঁপে বলির পাঠার মতো। কোনো রকমে ছুটির ঘণ্টা পড়ে গেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। তারপর পড়ি মাধব পণ্ডিতের কাছে। বাংলা, সংস্কৃত পড়ান; অতি অমায়িক ভটচাজ্জি চেহারা, শিশুবোধের চাণক্য পণ্ডিতের ছবিখানি—মস্ত টিকি। সেই সময়ে একবার দিনে তারা উঠল, হঠাৎ ইস্কুল ছুটি হয়ে গেল। ছুটে সবাই বাইরে এলুম। ইস্কুলে একটা টেলিস্কোপ ছিল, তাই নিয়ে তারা দেখতে ঠেলাঠেলি লেগে গেল। সেই মাধব পণ্ডিতের কাছে পড়ি ‘পত্র পততি’, এমনি সব নানা সাধুভাষার বুলি। সেখান থেকে হেডমাস্টারের হাতে-পায়ে ধরাধরি করে অতিকষ্টে উঠলুম তো হরনাথ পণ্ডিতের কেলাসে। তাঁর চোয়াল দুটাে কেমন অদ্ভুত চওড়া, আর শক্ত রকমের। কথা যখন বলেন চোয়াল দুটে ওঠে পড়ে, মনে হয় যেন চিবোচ্ছেন কিছু। তাঁর কাছে পড়লুম কিছুদিন। এই করতে করতে তিনটে শ্রেণী উঠে গেছি। এইবার মাস্টার মশায়ের হাতে পড়ার পালা। এখন সেই শ্রেণীতে আসেন এক ইংরেজি পড়াবার মাস্টার। তিনি এক ইংলিশ রীডার লিখে বই ছাপিয়ে তা পাঠ্যপুস্তক করিয়ে নিয়েছিলেন। সেই বই আমাদের পড়তে হয়। একদিন হয়েছে কি—ক্লাসে ইংরেজির মাস্টার আমাদের পড়ালেন p-u-d-d-i-n-g—পাডিং। আমার মাথায় কি বুদ্ধি খেলে গেল, বলে উঠলুম, ‘মাস্টারমশায়, এর উচ্চারণ তো পাডিং হবে না, হবে পুডিং, আমি যে বাড়িতে এ জিনিস রোজ খাই।’ মাস্টার ধমকে উঠলেন, ‘বল পাডিং।’ আমি বলি, ‘না পুডিং।’ তিনি যত বলতে বলেন পাডিং, আমি আমার বুলি ছাড়িনে। বা রে, আমি পুডিং খাই যে, পাডিং বলতে যাব কেন? মাস্টার গোঁ ধরলেন পাডিং বলবেনই। আমি বলে চলি পুডিং। বাকি ছেলেরা থ হয়ে বসে দেখে কি হয় কাণ্ড। এই করতে করতে ক্লাসের ঘণ্টা শেষ হল। শাস্তি দিলেন চারটের পর এক ঘণ্টা ‘কনফাইন’। ইস্কুল ছুটি হয়ে গেল; বাড়ির গাড়ি নিয়ে রামলাল অপেক্ষা করছে দরজার সামনে। কিন্তু ‘কনফাইন’, এক ঘণ্টার আগে যেতে পারিনে। মাস্টার নিজের বৈকালিক সেরে এলেন। ঘরে ঢুকে বললেন, ‘এবারে বল্ পাডিং।’ উত্তর দিলেম, ‘পুডিং’। যেমন শোনা টানাপাখার দড়ি দিয়ে হাত দুটো বেঁধে তবে রে ব্যাদ্ড়া ছেলে, বলবিনে? বলতেই হবে তোকে পাডিং। দেখি কেমন না বলিস!’ বলে সপাসপ জোড়া বেত লাগালেন পিঠে। বেতের ঘায়ে পিঠ হাত লাল হয়ে গেল—তখনও বলছি পুডিং। রামলাল ব্যস্ত হয়ে বারে বারে দরজায় উঁকি দিয়ে দেখে, এ কি কাণ্ড হচ্ছে! যা হোক, বাড়ি এলাম। ছোটপিসিমা বললেন, ‘কি ব্যাপার?’ রামলাল বললে, ‘আমার বাবু আজ বড্ড মার খেয়েছেন।’ আমিও জামা খুলে পিঠ দেখালুম, হাত দেখালুম। দড়ির দাগ বসে গিয়েছিল হাতে। বাবামশায় তৎক্ষণাং নৰ্ম্যাল স্কুল থেকে নাম কাটাবার হুকুম দিলেন; বললেন, ‘কাল থেকে ছেলেরা বাড়িতে পড়বে।’ চুকে গেল ইস্কুল যাবার ভয়; জোড়া বেত খেয়ে ছাড়া পেলুম। এক ‘পাডিং’এই ইংরেজি বিদ্যে শেষ। পরদিন থেকে বাড়িতে বাবামশায়ের মাস্টার যদু ঘোষাল আমায় পড়াবার ভার নিলেন।
০৩. এখন স্কুলে যাওয়া বন্ধ
এখন স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে নামকাটা সেপায়ের কি বিপদ হল শোনো। স্কুলে যাওয়ার থেকে তো নিস্তার পেলুম, ভাবলুম বেশ হল, এবার বড়দের মতোই বুঝি আমি স্বাধীন হয়ে গেলুম। যা ইচ্ছে তাই করতে পারব, স্নানের জন্য, ভাত খাবার জন্য চাকররা আর তাড়া দেবে না। নিয়মমতো চলবারও দরকার হবে না। লম্বা পুজোর ছুটি, গরমের ছুটি পেলে যেমন আনন্দ হয় তেমনি আনন্দে দিন কাটবে বুঝি। কবে স্কুল খুলবে সে ভয়ও নেই। এই সব ফুর্তিতেই মাতলুম।
কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই দেখি, ওমা, তা তো নয়। যদু ঘোষাল মাস্টার বাড়িতেই থাকেন; ঠিক সময়ে পড়তে বসতে হয় তাঁর কাছে। দশটা বাজলেই চাকররা তাড়া লাগায়। স্নান করে খেয়ে নিতে হয় চটপট। খেয়েদেয়ে ঘুর্ ঘুর্ করি। স্কুল ছুটি তো শুধু আমারই হয়েছে। দাদা, ইন্দুদা ওঁরা সবাই চলে যান ইস্কুলে। ভেবেছিলেম, বেশ খেলাধুলো হুটোপাটি করে সময় কাটবে রোজ। তা আর হয় না। খেলব কার সঙ্গে? খেলার সাথীরা সবাই স্কুল করে, আমি একলা ঘরে কি করি ভেবে পাইনে। চাকররা থাকে তাদের কাজে ব্যস্ত। রামলাল ধমক দেয়, ‘কোথাও যেয়ো না, চুপটি করে বসে থাকো। এদিকে ওদিকে গেছ কি মুশকিল হবে বলে দিচ্ছি। গলির মোড়ে ওই ওইখানে কন্ধকাটা আছে,ধরে নেবে।’ বলে গলির মোড়ে একটা বাসাবাড়ির নিচে ড্রেনের খিলেন ছিল, সেইটে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। আগে অন্দরে যেতে পারতুম যখন-তখন। আজকাল সেই যে চাকররা সকালবেলা আমায় বের করে আনে অন্দর থেকে, সারাদিনে আর ভিভরে ঢুকবার হুকুম নেই, তবু দু-এক ফাঁকে ঢুকে পড়ি অন্দরে। মা ব্যস্ত ছোটভাইকে নিয়ে। সুনয়নী বিনয়নী ছোটবোন—তাদের সঙ্গে খেলতে খেলতে খেলনা একটা ভেঙে গেল কি তারা কাঁদতে শুরু করে দিলে, ‘অ্যাঁ, অবনদাদা আমাদের পুতুল ভেঙে দিলে।’ অমনি তাড়া লাগায় আমায় সকলে, ‘তুই এখানে কেন? যা বাইরে যা। সেখানে গিয়ে খেলা কর্।’ তাড়া খেয়ে বাইরে চলে আসি। বাইরে এসে ভাবের লোক আর পাইনে কাউকে। সবাই দেখি তাড়া লাগায়, ধমক দেয়।
বাবামশায়ের ছিল পোষা একটি কাকাতুয়া গোলাপী রঙের। বারান্দার দেয়ালে-টাঙানো হরিণের শিঙের উপর বসে থাকে, কি সুন্দর লাগে দেখতে। সকালবেলা মা পান সাজেন; মার কাছে গিয়ে পানের বোঁটা খায়। ছোটপিসিমার কাছে ছোলা খায়; আবার এসে শিঙের উপর উঠে বসে। ভাবলুম এবার মানুষ ছেড়ে পশুপাখির সঙ্গেই ভাব করা যাক। এই ভেবে কাকাতুয়ার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই ঝুঁটি তুলে গায়ের পালক ফুলিয়ে সে এল তেড়ে আমায় ঠোকরাতে। ভাব করা থাকুক পড়ে, ছুটে পালিয়ে বাঁচি সেখান থেকে। তার ডানার তলায় তলায় বাবামশায় নিজের হাতে পাউডার মাখান। পাউডার মেখে সে মেমসাহেব হয়ে ঝুঁটি বাগিয়ে বসে থাকে। গুমোর কি তার। সে করবে আবার আমার সঙ্গে ভাব। ভয়ে আর সেদিক দিয়েই যাইনে।
বাবামশায়ের আদরের কুকুর কামিনী। কি তার আদরযত্নের ঘটা। কামিনীর জন্য আলাদা চাকর মেথর। তাকে যখন সাবান দিয়ে পরিষ্কার করে স্নান করিয়ে, গায়ে পাউডার মাখিয়ে, পরিপাটি করে আঁচড়ে সিঁথি কেটে, সাজিয়েগুজিয়ে ছেড়ে দেয়, আর কামিনী ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়ায়, যেন বাড়ির খেঁদি মেয়েটি। বাড়ির ছেলে আমাদেরও অত আদরযত্ন হয় না যত হয় কামিনীর। সেই কামিনীর কাছে যাই। সে আমায় তোয়াক্কাই করে না। লেজ নেড়ে চলে যায় বাবামশায়ের ঘরের দিকে।
ছোট্ট ছোট্ট এক জোড়া পোষা বাঁদরও আছে বাবামশায়ের। কত তাদের আদরই বা। গ্রেট ঈস্টার্ন্ হোটেল থেকে বাঁদরের জন্য স্পেশাল লাল টুকটুকে চেরি আসে চিনিমাখানো। বাবামশায় একটি একটি করে ওই চেরি খাওয়ান তাদের। দেখে হিংসেয় জ্বলে মরি। ভাবি ওই চেরিগুলো নিজেরা যদি খেতে পাই, আঃ। তাঁর শখের হরিণও আছে একটি, নাম গোলাপী। গোলাপীর কাছে গেলে মালী আসে হৈ-হৈ করে।
দেখো এমন আমার কপাল! পশুপাখির কাছেও পাত্তা পাইনে। ওই একটু যা আদর পাই ছোটপিসিমার কাছে। মাঝে মাঝে তাঁর ঘরে আমায় ডেকে নেন। সেখানে কথকতা হয় রোজ। মাইনে-করা মহিম কথক আছেন। বসে শুনি খানিক। কিন্তু তাও আর কতক্ষণই বা! মহামুশকিল, একলা একলা সময় আর কাটে না। মনের দুঃখে ভাবি, এর চেয়ে বেশ ছিলুম স্কুলেই। গাড়িতে ওঠবার আগেই যত কান্নাকাটি, উঠেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যেত। গাড়ি চলত গলির মোড় ঘুরে। সেই শিবমন্দির, কাঁসরঘণ্টা, লোকজন, দোকানপাট, রাস্তার দুদিক দেখতে দেখতে বেশ যেতম। তবুও তো বাইরের জগৎ দেখতে পেতুম কিছুটা; এখন কোন বন্ধখানায় পড়লুম! ফটক পেরিয়ে ওদিকে যাবারই আর উপায় নেই। খোলা ফটক আগলে বসে আছে মনোহর সিং দারোয়ান দেউড়িতে। মনে পড়ে স্কুলের সামনে প্রতাপের লজেঞ্জুসের দোকান। চেয়ে নিয়ে ছোট্ট ছোট্ট হলদে লাল সবুজ লজেঞ্জুস খেতুম। চাইলেই দুটি-একটি হাতে গুঁজে দিত প্রতাপ।
আর মনে পড়ে সমবয়সীদের কথা । তাদের নিয়ে হুটোপাটি করেও মন্দ ছিলুম না। আমারই মতো ডানপিটে ছেলেও ছিল একটি-দুটি। একটির কথা বলি, স্কুলে যেতে তারও ছিল বেজায় আপত্তি। স্কুলে যাবার সময় হলেই সে পালিয়ে বেড়ায়। একদিন স্কুলে যাবার সময় হয়েছে; সে এদিকে করেছে কি, বাড়ির পাশেই এক শিবমন্দির, তার ভিতরে ঢুকে কাপড়জামা খুলে অন্ধকার ঘরে কালো পাথরের শিবকে জড়িয়ে ধরে বসে রইল। ছেলেটির রঙও কালো, শিবের কালোয় তার কালোয় মিশে গেল। চাকরবাকররা আর খুঁজে তাকে পায় না। মহা হৈ-চৈ। শেষে কে একজন শিবের মাথায় জল ঢালতে গিয়ে তাকে আবিষ্কার করলে। সেই সব সঙ্গীর কথা মনে পড়ে, আর মন খারাপ হয়ে যায়।
নর্ম্যাল স্কুলের বাড়িটিও ছিল কেমন রহস্যময়। প্রকাণ্ড রাজবাড়ি; তাতে কত অলিগলি, অন্দিসন্দি, এখানে ঘর, ওখানে খিলেনদেওয়া বারান্দা, মোটা মোটা থাম; তারি গায়ে দিনের আলো পড়ে চক্চক্ করত। ঘুরে ঘুরে দেখতুম এই সব। কোথায় গেল আমার সেই নর্ম্যাল স্কুল! বহুকাল পর এই সেদিন কোন্ এক সিনেমাতে দেখলুম সেই বাড়ির ছবি। দেখে ভারি মজা লাগল। যাক সে কথা। এখন আমার একলা থাকার গল্পটাই বলি।
সকালবেলাটা লেখাপড়ায় যদিই বা কোনোমতে কেটে যায়, দুপুর আর কাটে না। দাদারা চলে যান স্কুলে, বাবামশায় যান কাছারিতে। ফার্সি পড়াবার মুনশী আসেন; দু-চারটে আ লে বে পড়িয়ে চলে যান। এই মুনশীই দাঁড়িয়ে দেয়ালে নিজের ছায়ার সঙ্গে লড়াই করতেন। একদিন লড়াই করতে গিয়ে রোখের মাথায় ছায়াতে যেমন ঢুঁ-মারা অমনি মুনশীর কপাল ফেটে রক্তপাত। চাকররাও তাদের তোষাখানায় গল্পগুজব করে। বৈঠকখানা শোনশান, একলা আমি সেখানে পড়ে থাকি। থেকে থেকে দাদাদের ডেক্সোর ঢাকা তুলে দেখি ভিতরে কি আছে। নেড়েচেড়ে দেখে আবার তেমনি সব ঠিকঠাক রেখে দিই। প্রাণে ভয়, যদি জানতে পারেন হয়তো বকুনি দেবেন। বাবামশায়ের টেবিলটা দেখি। কতরকম রঙ তার উপরে সাজানো। একটা ক্রিস্ট্যালের কলমদানি ছিল, ঠিক যেন সমুদ্রের ঝিনুক একটি। সেইরকম নকশায় গোলবাগানে ফোয়ারা তৈরি করিয়েছিলেন বাবামশায়। এখনও তা আছে। সেদিন যখন গেলুম জোড়াসাঁকোয়, দেখি বাগানের সব কিছু ভেঙে কেটে নষ্ট করে ফেলেছে, একটি গাছও বাকি রাখেনি; কিন্তু ফোয়ারাটি তেমনি আছে সেখানে, ফটিক জলে ভরতি। টেবিলে সেই কলমদানিতে কলম সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সেটাতে একবার হাত বুলোই, আবার এসে শুয়ে থাকি। তাও কোথায় শুয়ে থাকতুম জানো? বিলিয়ার্ড টেবিলের নিচে। মাকড়সার জাল, ধুলো বালি, কত কি সেখানে। শুয়ে শুয়ে দেখি মাথার উপরে ঝুলছে সেসব। শোবার জায়গা আমার ওই রকমেরই। ছেঁড়া মাদুরের উপরে, কৌচ-টেবিলের তলায় তলায়, ঢুকে শুয়ে থাকি। ঠিক যেন একটা জানোয়ার। বুদ্ধিও কতকটা আমার তেমনি। তবে একলা থাকার গুণ আছে একটা। দেখতে শুনতে শেখা যায়। ওই অমনি করে একলা থাকতে থাকতেই চোখ আমার দেখতে শিখল, কান শব্দ ধরতে লাগল। তখন থেকেই কত কি বস্তু, কত কি শব্দ যেন মন-হরিণের কাছে এসে পৌঁছতে লেগেছে। মানুষ, পশুপাখি সঙ্গী পেলেম না কাউকেই। ওই অত বড় বাড়িটাই তখন আমার সঙ্গী হয়ে উঠল; নতুন রূপ নিয়ে আমার কাছে দেখা দিতে লাগল। এখানে ওখানে উঁকিঝুঁকি দিয়ে তখন বাড়িটার সঙ্গে আমার পরিচয় হচ্ছে। জোড়াসাঁকোর বাড়িকে যে কত ভালো বেসেছি। বলি যে, ও বাড়ির ইটকাঠগুলিও আমার সঙ্গে কথা কয়, এত চেনাপরিচয় তাদের সঙ্গে; তা ওই তখন থেকেই তার শুরু। পড়ে আছি; দেখছি, ঘরের কোণায় কোথায় কার্নিশের ছায়া পড়েছে, কোথায় টিকটিকিটা পোকা ধরবার জন্য ওত পেতে আছে, চড়ুইপাখি ছোট কুলুঙ্গিতে বাসা বাঁধছে। আবার কোথায় কোন্ উঁচুতে ছাদের উপরে লোহার শিকে এক চিল বসে আছে তাকে দেখছি তো দেখছিই। একসময়ে সে চিঃ-ঃ-ঃ করে দুটো চক্কর খেয়ে উড়ে গেল। আবার কখনো বা চেয়ে থাকতুম সামনে সাদা দেওয়ালের দিকে, ওপাশের উত্তরের খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে দিনের আলো এসে পড়েছে তাতে; বাইরে মানুষ হেঁটে যায়, ছায়াটিও চলে যায় ঘরের ভিতরে দেয়ালের গা দিয়ে। রঙিন এক-একখানি ছবির মতো তারা আলোর রাস্তা ধরে চলতে চলতে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়। এই ছবি-দেখা রোগ আমার এখনো আছে, দিনে দুপুরে ঘরের ভিতরে বসে বসে ছবি দেখি। কাল দুপুরে কৌচে বসে ঝিমোচ্ছি। বাইরের তালগাছের ছায়া এসে পড়েছে দেয়ালে, পাতাগুলি নড়ছে হাওয়াতে, পিছনের আকাশে সাদা মেঘ—ঠিক যেন চাঁদের আলোর ছবি একটি। তখনও সব দেখতুম, একমনে দেখতুম। এই দেখতে যখন আরম্ভ করলুম তখন আর একলা থাকতে খারাপ লাগত না।
এদিকে আবার নানারকম শব্দও আসে কানে, দুপুর হতেই গলির মোড়ে শব্দ হল ঠং ঠং, ‘বাসন চাই বাসন।’ শব্দ চলে গেল দূরে। তার পরে এল ‘চুড়ি চাই, খেলনা চাই।’ প্রায়ই মায়েদের মহলে তাদের ডাক পড়ে, ঝুড়ি ঝুড়ি নান৷ রঙের কাচের চুড়ি সাজিয়ে বসে এসে। একরকমের মজার খেলনা থাকে তাদের ঝুড়িতে; টিনের এতটুকু এতটুকু মাছ আর চুম্বকের কাঠি। মাছটি জলে ভাসিয়ে চুম্বকের কাঠি দিয়ে টানলেই মাছও সঙ্গে সঙ্গে জলের উপর চলতে থাকে, এমন লোভ হয় ওই খেলনার জন্য। বাড়ির অন্য সব ছেলেমেয়েরা প্রায়ই পায় সেই খেলনা, আমি পাই ক্বচিং কখনো। আমাকে কেউ যে খেয়ালই করে না তেমন। তারপর বেলা পড়ে এলে গরমের দিনে বরফওয়ালা হেঁকে যায়, “বরিফ, বরিফ চাই, বরিফ–কুলপি বরিফ। জ্যোতিকাকা মশায় লিখেছিলেন একটা গান
‘বরিফ বরিফ’ ব’লে
বরফওয়ালা যান।
গা ঢালো রে, নিশি আগুয়ান।
‘বেল ফুল বেল ফুল’
ঘন হাঁকে মালীকুল—
সন্ধ্যাবেলার শব্দ হচ্ছে ওই বেলফুল। ‘বেলফুল চাই বেলফুল’ হাঁকতে হাঁকতে শব্দ গলির এদিক থেকে ওদিক চলে যায়। তাদের ডেকে বেলফুল কেনে দাসীরা, মালা গাঁথেন মেয়েরা।
ভরসন্ধ্যেবেলা মুশকিল আসান আসে খিড়কির দরজায় চেরাগ হাতে, লম্বা দাড়ি; পিদিম জ্বলছে মিটমিট করে। বারান্দ থেকে দেখি তার চেহারা। দোরগোড়ায় এসেই হাঁক দেয়, ‘মুশকিল আসান, মুশকিল আসান।’ দপ্তরে বরাদ থাকে, মুশকিল আসান এলেই তাকে চাল পয়সা যা হয় দিয়ে দেয়; সে আবার হাঁক দিতে দিতে চলে যায়।
আরও একটি শব্দ, সেটি এখনও থেকে থেকে কানে বাজে। দুপুরে সব যখন শোনশান, কোনো সাড়াশব্দ নেই কোথাও, তখন শব্দ কানে আসে ‘কূ-য়ো-র ঘটি তোলা’। মনে হয় ঠিক যেন অদ্ভুত কোন্ একটি পাখি ডেকে চলেছে। রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে জানালা দিয়ে দেখি ঘনকালো তেঁতুলগাছের মাথা। দাসীরা বলে, বংশের সকলের নাড়ী পোঁতা আছে তার তলায়, মাঝে মাঝে ছাতের উপরে ভোঁদড় চলে বেড়ায়, সেই চলার শব্দে গল্প তৈরি হয় মনের ভিতরে; ব্রহ্মদত্যি হাঁটছে, জটেবুড়ি কাসছে। জটেবুড়ি সত্যিই ছিল, লাঠি ঠক ঠক করে আসত; ময়ূরে তার চোখ উপড়ে নিয়েছিল। ‘ক্ষীরের পুতুল’এ যে ষষ্ঠী বুড়ি এঁকেছি ঠিক সেই রকম ছিল সে দেখতে।
ওদিকে নিচে রাত দশটার পর নন্দ ফরাসের ঘরে নোটো খোঁড়ার বেহালা শুরু হয়। একটাই সুর অনেক রাত্তির অবধি চলে একটানা। বেহালা যেন সুরে এক দুই মুখস্থ করছে; এক, দুই, তিন, চার; এক, দুই, তিন, চার। ওই থেকে পরে আমি একটা যাত্রার সুর দিয়েছিলুম। বাবামশায়ের বৈঠক ভাঙলে নন্দ ফরাসের ঘরে বৈঠক বসে—ছিরু মেথর, নোটো খোঁড়া, আরও অনেকের। ভোরবেলা বাড়ির সামনে ঘোড়া মলে টপ টপ ধপধপ। কাকপক্ষী ডাকার আগে এই শব্দ শুনেই ঘুম ভাঙে আমার। রোজ ঘুমোবার আগে আর ঘুম ভেঙে এই দুটি শব্দ শুনি—বেহালার এক, দুই, তিন, চার; আর ঘোড়ামলার টপ টপ ধপ ধপ।
তখন এক-একটা সময়ের এক-একটা শব্দ ছিল। এখন সেই শব্দ আর নেই। সব মিলিয়ে যেন কোলাহল চারদিকে। ট্যাক্সির ভোঁ-ভোঁ, দোকানদারের চিংকার, রাস্তার হট্টগোল, এসবে ঘরের কোণায়ও কান পাতা দায়। তার উপরে জুটেছে আজকাল মাথার উপরে উড়োজাহাজের ঘড়ঘড়ানি, রেডিওর ভনভনানি, আরও কত কি। তেতালার ছাদে জ্যোতিকাকামশায়ের পিয়ানোর সুর, রবিকার গান, জ্যাঠামশায়ের হাসির ধমক, কোথায় চলে গেল সে সব!
তা সেই সময়ে দুপুরে বৈঠকখানাতেই একদিন আমি আবিষ্কার করলুম ‘লণ্ডন নিউজে’র ছবি। বাঁধানো ‘লণ্ডন নিউজ’ পড়েছিল এক কোণায়। সব-কিছু ঘেঁটে ঘেঁটে দেখতে গিয়ে বইয়ের ভিতরে ছবির সন্ধান পেলুম। সে কতরকম কাণ্ডকারখানার ছবি, নিবিষ্ট মনে বসে বসে দেখি। একদিন ঘোষাল মাস্টার এসে ঢুকলেন সেই ঘরে। দিব্যি ভুঁড়িদার চেহারা তার; খালি গায়ে যখন আসেন, তেলচুকচুকে ভুঁড়িটি ঠিক যেন পিতলাই হাড়া একটি। তিনি ঘরে ঢুকে বললেন, ‘দেখি কি দেখছ’—বলে আমার হাত থেকে বইগুলি নিয়ে পাতা উলটে উলটে দেখতে লাগলেন। দেখতে দেখতে একটা পাতায় আছে ফরাসী রানীর ছবি, তিনি সেই ছবিটি সামনে রেখে হাতজোড় করে তিনবার মাথায় ঠেকালেন। তারপর থেকে দেখি রোজই তিনি স্নানের পর ফরাসী রানীর ছবি বের করে তিনবার পেন্নাম করেন। কারণ আর বুঝিনে কিছু। দেবদেবীর ছবি এ নয়, তবে কেন এত পেন্নামের ঘটা। শেষে বড়দাকে একদিন জিজ্ঞেস করি, ‘এর মানে কি বলে না।’ বড়দা হেসে বললেন, ‘ওহো তা বুঝি জানিসনে? ঘোষাল মশায়কে জিজ্ঞেস করেছিলুম যে, তিনি বললেন, এই ফরাসী রানী তাঁর স্ত্রীর মতো দেখতে। তাই রোজ তিনি ওই ছবিকে পেন্নাম করেন।’
০৪. ছেলেবেলায় খুব গান আর ছবি-আঁকা
সেদিন কে যেন আমায় বললে, আপনি বুঝি ছেলেবেলায় খুব গান আর ছবি-আঁকার আবহাওয়ায় বড় হয়েছেন? বললুম, মোটেও তা নয়। কি আবহাওয়ার ভিতর দিয়ে বড় হয়েছি জানতে চাইছ? শোনো তবে।
ছবি গান ছিল বইকি বাড়িতে। বাবামশায়ের শখ ছিল ছবি আঁকার; জ্যোতিকাকামশায়ও ছবি আঁকতেন, পোর্ট্রেট আঁকবার ঝোঁক ছিল তার; কিন্তু ছবি দেখা তো দূরের কথা, আমরা কি তাঁদের ঘরে ঢুকতে পেরেছি কখনও?
গানবাজনাও হত। তখনকার দিনে মাইনে-করা গাইয়ে থাকত বাড়িতে। কেষ্ট বিষ্ণু ছিল দুই মাইনে-করা গাইয়ে। দুর্গাপুজোয় আগমনী বিজয়া তখন গাইত তারা—শোননি কখনও? ভারি মিষ্টি সেসব গান। ওস্তাদি গানের মজলিশও বসত বৈঠকখানায় রোজ সন্ধ্যেবেলা। তখনকার নিয়মই ছিল ওই। পাড়াপড়শি বন্ধুবান্ধব আসতেন বৈঠকি গান শুনতে। নটার তোপও পড়ত, মজলিশও ভেঙে যে যার ঘরে যেতেন। দূর থেকে যেটুকু শুনতুম কিছুই বুঝতুম না তার।
তবে হ্যাঁ, গান হত ও-বাড়িতে, তেতলার ছাদে নতুনকাকিমার ঘরে। একদিকে জ্যোতিকাকামশায় পিয়ানো বাজাচ্ছেন, আর একদিকে রবিকা গাইছেন। সেই অল্পবয়সের রবিকার গলা, সে যেমন সুর তেমনি গান। মাত করে দিতেন চারদিক। এ-বাড়ি থেকে শুনতুম আমি কান পেতে। তাই বলি, গান তবু শুনেছি আমি ছেলেবেলায়; কিন্তু ছবি দেখিনি মোটেও।
ছবি যা দেখেছি তা আমার ছোটপিসিমার ঘরে। ছুটির দিন দুপুরবেলা ছোটপিসিমার ঘরের দরজায় একটু উঁকিঝুঁকি মারতেই ছোটপিসিমার নজরে পড়ি, তিনি ডাকেন, ‘কে রে অবা? আয় আয় ঘরে আয়।’ কি সুন্দর ঘরটি তাঁর। কতরকমের ছবি, দেশী ধরনের অয়েল-পেটিং, শ্রীকৃষ্ণের পায়েস ভক্ষণ— সামনে নৈবেদ্য সাজিয়ে মুনি চোখ বুজে ধ্যানে বসে আছেন, চুপি চুপি কৃষ্ণ হাত ডুবিয়ে পায়েসটুকু তুলে মুখে দিচ্ছেন, হুবহু কথকঠাকুরের গল্পের ছবি; শকুন্তলার ছবি—তিনটি মেয়ে বনের ভিতর দিয়ে চলেছে, শকুন্তলা বলে বুঝতুম না, তবে ভালো লাগত দেখতে; মদনভস্মের ছবি—মহাদেবের কপাল ফুঁড়ে ঝাঁটার মতো আগুন ছুটে বের হচ্ছে; সরোজিনী নাটকের ছবি; কাদম্বরীর ছবি—রাজপুত্তুর পুকুরধারে গাছতলায় ঘোড়া বেঁধে শিবমন্দিরের দাওয়ায় বসে আছে। কে জানে তখন, সেটা কাদম্বরীর ছবি। এমনি কত সব ছবি। কেষ্টনগরের পুতুলই বা কত রকমের ছিল সেই ঘরে। চেয়ে চেয়ে দেখতে বেলা কাটে। মেঝেতে ঢালা-বিছানায় বুকে বালিশ দিয়ে বসে ছোটপিসিমা পান খান, সেলাই করেন। ও-বাড়িতে বেলা তিনটের ঘণ্টা পড়ে। গুপীদাসী চুল বাঁধার বাক্স, মাদুর নিয়ে আসে। ছোটপিসিমা উঠে উঁচু-পাঁচিল-ঘেরা ছাদে গিয়ে চুল বাঁধতে বসেন, পোষা পায়রাগুলো খোপ থেকে বেরিয়ে এসে ছোটপিসিমাকে ঘিরে ঘাড় নেড়ে বকম বকম বকে বকে নাচ দেখায়। ছোটপিসি আমার হাতে মুঠো মুঠো দানা দেন; ছড়িয়ে দিই, তারা চক্কর বেঁধে কুড়িয়ে কুড়িয়ে খেয়ে উড়ে বসে ছাদের কার্নিশে সারি সারি। পড়ন্ত রোদ তাদের ডানায় ডানায় ঝকমক করে। কোনো কোনো দিন বা দেখি ঘূর্নি হাওয়ায় লাল ধুলো পাক খেয়ে খেয়ে উড়ে গেল। বাইরের ছবিও দেখি। আবার খেলাধুলোর শেষে ঘরের কোণায় সন্ধ্যেবেলা পিতলের পিলসুজের উপর পিদিম জলে, তারই কাছে টিকটিকি নড়েচড়ে পোকা ধরে, তাও দেখি চেয়ে চেয়ে অনেকক্ষণ। এইরকম ঘর-বাইরের কত কি ছবি দেখতে দেখতে বেড়ে উঠেছি।
ভিতর দিকটা দেখবার কৌতুহল আমার ছেলেবেলা থেকে আছে। বন্ধ ঘরের ভিতরটা, ঘেরা বাগানের ভিতরটা, দেখতে হবে কি আছে ওখানে। খেলনা, দম দিলে চলে চাকা ঘোরে; দেখতে চাই ভিতরে কি আছে। এই সেদিন পর্যন্তও ছেলেদের খেলনা নিয়ে খুলে খুলে আবার মেরামত করেছি। ছেলেদের খেলনা হাতে নিলেই মা বলতেন, “ওই রে এবার গেল জিনিসটা, ভিতর দেখতে গিয়ে ভাঙবে ওটি।’ তা ছেলেবেলায় একবার ভিতর দেখতে গিয়ে কী কাণ্ডই হয়েছিল শোনো।
বড়মা থাকেন তেতলার একটি ঘরে। তাঁরও নানারকম পাখি পোষার শখ। পোষা টিয়ে, পোষা লালমোহন হীরেমোহন; লালমোহনের দাঁড়টি আগাগোড়া ঝকঝক তকতক করছে সোনালি রঙে। ঘরের একপাশে এক আলমারি বোঝাই খেলনা; সে-সব তাঁর শখের খেলনা, কাউকে ধরতে ছুঁতে দেন না। অনেক ক’রে বললে কখনও একটা-দুটাে খেলনা বের করে নিজের হাতে দম দিয়ে চালিয়ে দেন মেঝেতে; আবার তুলে রাখেন। সেই বড়মার ঘরে যেতে হত একটি মেটে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে। বরাবর তেতলার চিলে-ছাদ অবধি উঠে গেছে সেই গোল সিঁড়ি। তারই মাঝামাঝি এক জায়গায় মাটির একটি হাতদেড়েক কেষ্টমূর্তি, তাকের উপর ধরা। আমার লোভ সেই মাটির কেষ্টটির উপর। একদিন দুপুরে সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে বড়মার কাছে দরবার করলুম, “আমাকে মাটির কেষ্টটি দেবে? বড়মা খানিক ভেবে বললেন, ‘চাস? তা নিয়ে যা। ভাঙিসনে।’ বুড়ী দাসী তাক থেকে কেষ্টটি পেড়ে আমার হাতে দিলে। আমি সেটি বগলদাবা করে তরতর করে নিচে নেমে এলুম। দাদাদেরও নজর ছিল মূর্তিটির উপর, কেউ পাননি। তাদের দেখালুম। ‘দেখো, তোমরা তো পেলে না; আমি কেমন পেয়ে গেছি।’ দাদারা বললেন, ‘হুঃ, ওর ভিতরে কি আছে জানিসনে তো? এই টেবিলটির উপরে চড়ে মূর্তিটি ফেলে দে নিচে, দেখবি, আশ্চর্য জিনিস বের হবে এর ভিতর থেকে।’ দাদাদের অবিশ্বাস করতে পারলেম না। মূর্তির ভিতরের ‘আশ্চর্য’ দেখবার লোভে তাড়াতাড়ি উঁচু টেবিলটায় উঠে দিলেম কেষ্টকে মাটিতে এক আছাড়। ‘আশ্চর্য’ তো দেখা দিল না ; মাটির পুতুল ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ঘরময়। তথন আমার কান্না, দাদার হো-হো করে হেসে হাততালি দিয়ে চম্পট।
সেই ভিতর দেখার কৌতুহল আজও আমার ঘুচল না। ছবি, তার ভিতরে কি আছে খুঁজি। নোড়ানুড়িতে খুঁজি, কাঠকুট্রোতে খুঁজি। নিজের আর অন্যের মনের ভিতরে খুঁজি, কি আছে না-আছে। খুজি, কিছু পাই না-পাই, এই রকম খোঁজাতেই মজা পাই। হাত আমার তখন ভালো করে পেনসিল ধরতে পারে না, ছবি আঁকা কাকে বলে জানিনে; কিন্তু ছবি দেখতে ভাবতে শিখি সেই পিসিমার ঘরে বসে।
মার ঘরে আমরা ঢুকতে পাইনে। মার ঘর একেবারে আলাদা ধরনে সাজানো। মার শোবার ঘর তৈরি হচ্ছে। রাজমিস্ত্রি লেগে গেছে; বাবামশায়ের পছন্দমতো মেঝেতে নানা রঙের টালি পাথর বসানো হচ্ছে, আস্তে আস্তে যাই সেখানে। ঠুকঠাক, মিস্ত্রিরা নকশা মিলিয়ে পাথর বসায়; অবাক হয়ে দেখি। কখনো বা দু-একটা পাথর চেয়ে আনি। দেখতে দেখতে একদিন ঘর তৈরি হয়ে গেল। বাবামশায় নিজের হাতে সে ঘর সাজালেন। চমৎকার সব পালিশ-করা দামী কাঠের আসবাবপত্র, কাটা কাচের নানারকম ফুলদানি, একটি ফুলদানি মনে পড়ে ঠিক যেন পদ্মকোরকটি,—কাচের গোরু-হাতি, কত কি। দেয়ালে দামী দামী অয়েল-পেন্টিং, চারিদিকে নানা জাতের অর্কিড, সে একেবারে অন্য রকমের সাজানো ঘর। আমার কিন্তু ভালো লাগে বেশি ছোটপিসিমার ঘরখানিই। বঙ্কিমবাবুর সূৰ্যমুখীর ঘরের যে বর্ণনা, যেখানে যে জিনিসটি, হুবহু আমার ছোটপিসিমার ঘরের সঙ্গে মিলে যায়। অত বড় বাড়ির মধ্যে আমার শিশুমনকে খুব টানত তেতলার উপর আকাশের কাছাকাছি ছোটপিসিমার ঘর।
আর একটি জায়গা, সেটি আমার পরীস্থান। দেখো, যেন শুনে হেসে না। আমার পরীস্থান আকাশের পারে ছিল না। ছিল একতলায় সিঁড়ির নিচে একটা এঁদো ঘরের মধ্যে। সেই ঘরে সারাদিনরাত বন্ধ থাকে দুয়োর, মস্ত তালা। ওত পেতে বসে থাকি সকাল থেকে, বড় সিঁড়ির তলায় দোরগোড়ায়। নন্দফরাশ আমাদের তেলবাতি করে, তার হাতে সেই তালাবন্ধ ঘরের চাবি। সে এসে সকালে তালা খোলে তবে আমি ঢুকতে পাই সেই পরীস্থানে। সেখানে কি দেখি, কাদের দেখি? দেখি কর্তাদের আমলের পুরোনো আসবাবপত্রে ঠাসা সে ঘর। কালে কালে ফ্যাশান বদল হচ্ছে, নতুন জিনিস ঢুকছে বাড়িতে, পুরনোরা স্থান পাচ্ছে আমার সেই পরীস্থানে। কত কালের কত রকমের পুরোনো ঝাড়লণ্ঠন, রঙবেরঙের চিনে মাটির বাতিদান, ফুলদানি, কাচের ফানুষ, আরও কত কি। তারা যেন পুরাকালের পরী—তাকের উপর সারি সারি চুপচাপ, ধুলো গায়ে, ঝুলমাকড়শার জাল মুড়ি দিয়ে বসে আছে; কেউ বা মাথার উপরে কড়ি থেকে ঝুলছে শিকল ধরে। ঘরের মধ্যেটা আবছা অন্ধকার। কাচমোড় ঘুলঘুলি থেকে বাইরের একটু হলদে আলো এসে পড়েছে ঘরে। সেই আলোয় তাদের গায়ে থেকে থেকে চমক দিচ্ছে রামধনুর সাত রঙ। আঙুল দিয়ে একটু ছুঁলেই টুং টাং শব্দে ঘর ভরে যায়। মনে হয়, যেন সাতরঙা সাত পরীর পায়ে ঘুঙুর বাজছে। সেই রঙবেরঙের পরীর রাজত্বে ঢুকে এটা ছুঁই ওটা ছুঁই, একে দেখি তাকে দেখি, কাউকে বা হাতে তুলে ধরি, এমন সময়ে নন্দফরাশ তার তেলবাতি সেরে হাঁক দেয়, ‘বেরিয়ে এসো এবারে, আর নয়, কাল হবে।’ তালাচাবি পড়ে যায় সেদিন রাতটার মতো আমার পরীরাজত্বের ফটকে।
সেই যেবার মুকুলের স্কুলে রবিকার ছবির এক্জিবিশন হয়, আমি দেখতে গছি ; অমিয় বললে, “আমায় গুরুদেবের ছবি বুঝিয়ে দিন।’ বললুম, দেখে বাপু, খুড়ো-ভাইপোর কথা কাগজে যদি বের না করো তবে এসো আমার সঙ্গে।’ তাকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে ছবি দেখাতে লাগলুম। তা ওইখানেই একটি ছবি দেখি; ছোট্ট ছবিখানা, কলম দিয়ে আঁকা; একটি ছেলে, পিছনে অনেকগুলো লাইনের আঁচড়। ছেলেটি লাইনের জালে আর জঙ্গলে আটকে পড়ে থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বললুম অমিয়কে, ‘দেখো, এ কি আর সবাই বুঝতে পারে?’ পরীস্থানে ঢুকলে আমার অবস্থা হত ঠিক তেমনি। এখন যখন দেখি ছোট ছেলেরা এসে আমার পুতুলের ঘরে কাচমোড়া আলমারির সামনে ঘুরঘুর করে, মনে পড়ে আমিও একদিন প্রায় এদেরই বয়েসে আমার পরীরাজত্বের দুয়োরে এমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকতুম।—ও অভিজিৎ, রঙ-টঙ নিয়ে অত ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না,—বিপদ আছে। এই রঙ-করা নিয়ে আমার ছেলেবেলায় কি কাণ্ড হয়েছে জানো না তো?
আমাদের দোতলার বারান্দায় একটা জলভরতি বড় টবে থাকে কতকগুলো লাল মাছ, বাবামশায়ের বড় শখের সেগুলো। রোজ সেই টবে ভিস্তি দিয়ে পরিষ্কার জল ভরতি করা হয়। একদিন দুপুরে লাল মাছ দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার খেয়াল হল, লাল মাছ, তার জল লাল হওয়া দরকার। যেমন মনে হওয়া কোত্থেকে খানিকটে মেজেণ্ট না কি রঙ জোগাড় করে এনে দিলুম সেই মাছের টবে গুলে। দেখতে দেখতে আমার মতলব সিদ্ধি। লাল জলে লাল মাছ কিলবিল করতে থাকল। দেখে অন্য খেলা খেলতে চলে গেলাম। বিকেলে শুনি। মালীর চিৎকার। জলে লাল রঙ গুললে কে? মাছ যে মরে ভেসে উঠেছে। বাবামশাই বললেন, ‘কার এই কাজ?’ সারদা পিসেমশায় বলে উঠলেন, ‘এ আর কারো কাজ নয়, ঠিক ওই বোম্বেটের কাজ।’ বোম্বেটে কথাটি চীনে গিয়ে সারদা পিসেমশায় শিখে এসেছিলেন। চীনের খেতাব সেইবারই প্রথম পেলুম; তার পর থেকে সবার কাছে ওই নামেই বিখ্যাত হলুম। রঙ গুলে আমি ওইরূপ খেতাব পেয়েছিলেম। অভিজিৎ, বুঝে-শুনে আমার রঙের বাক্সে হাত দিও। না হলে খেতাব পেয়ে যাবে।
আঃ হাঃ, আবার আমার পুতুল গড়বার হাতুড়ি বাটালি নিয়ে টানাটানি কর কেন? স্থির হও, শোনো, আর একটা মজার কথা। ছেলেবেলায় তোমার বয়সে মিস্ত্রি হবার চেষ্টা করেছিলুম একবার। বাবামশায়ের পাখির খাঁচা তৈরি হচ্ছে। খাঁচা তো নয়, যেন মন্দির। বারান্দা জুড়ে সেই খাঁচা, ভিতরে নানারকম গাছ, পাখিদের ওড়বার যথেষ্ট জায়গা, জলখাবার সুন্দর ব্যবস্থা, সব আছে তাতে। চীনে মিস্ত্রিরা লেগে গেছে কাজে; নানারকম কারুকাজ হচ্ছে কাঠের গায়ে। সারাদিন কাজ করে তারা টুকটাক টুকটাক হাতুড়ি বাটালি চালিয়ে দুপুরে খানিকক্ষণের জন্যে টিফিন খেতে যায়; আবার এসে কাজে লাগে। আমি দেখি, শখ যায় অমনি করে বাটালি চালাতে। একদিন, মিস্ত্রিরা যেমন রোজ যায়, তেমনি খেতে গেছে বাইরে, এই ফাঁকে আমি বসে হাতুড়ি বাটালি নিয়ে যেই না মেরেছি কাঠের উপর এক ঠেলা, এই দেখো সেই দাগ, বাটালি একেবারে বাঁ হাতের বুড়ে আঙুলের মাঝ দিয়ে চলে গেল অনেকটা অবধি। তখনি আমি বুড়ো আঙুল চুষতে চুষতে দে ছুট সেখান থেকে। মিস্ত্রিরা এসে কাজ করতে যাবে দেখে, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত সে জায়গায় ছড়ানো। কি ব্যাপার, কে কি কাটল? জানা কথা, বোম্বেটে ছাড়া এ আর কারোর কাজ নয়। বাবামশায় ডেকে বললেন, ‘দেখি তোর আঙুল।’ আমি তো ভয়ে জড়োসড়ো, না জানি আজ কি ঘটে যায় আমার কপালে।
কতরকম দুষ্টবুদ্ধিই জগত তখন মাথায়। বাবামশায়ের আছে পোষা ক্যানারি, খাঁচাভরা। শখ গেল তাদের ছেড়ে দিয়ে দেখতে হবে কেমন করে ওড়ে। টুনিসাহেব, এক ফিরিঙ্গি ছোঁড়া, আসে প্রায়ই বাবামশায়ের কাছে শ্রীরামপুর থেকে। পাখির শখ ছিল তার। মাঝে মাঝে সুবিধেমতে দুয়েকটি দামী পাখিও সরায়। সেই সাহেব একদিন এসেছে; তাকে ধরে পড়লুম, ‘দাও না ক্যানারি পাখির খাঁচা খুলে। বেশ উড়বে পাখিগুলো। জাল আছে এখানে, আবার ওদের ধরা যাবে।’ অনেক বলাকওয়ার পর সাহেব তো দিলে খাঁচার দরজা খুলে। ফুর্ ফুর্ করে পাখিগুলো সব বেরিয়ে পড়ল—খাঁচা থেকে বাইরে, মহা আনন্দ। এবার তাদের ধরতে হবে, টুনিসাহেব জাল ফেলছে বারে বারে; কিছুতেই তারা ধরা দেয় না। শেষে সে তো জাল-টাল ফেলে দিয়ে চম্পট; ধরা পড়লুম আমি। এইরকম সব ইচ্ছে ছেলেবয়েসে হত। ইচ্ছে হল কাঠবেড়ালির চলা দেখব, খরগোশের লাফ দেখব, অমনি তাদের ঘরের দরজা খুলে নিতুম বাইরে বের করে। ইচ্ছে হত তো, করব কি, কি বল অভিজিৎ?
ও কি ও, স্যাঙাত, সোয়েটার এঁটে এসেছ এরই মধ্যে? আমাদের ছেলেবেলায় কার্তিক মাসের আগে গরম কাপড়ের সিন্দুকই খুলত না ম্যালেরিয়া হলেও। সাদাসিধে ভাবেই মানুষ হয়েছি আমরা। তখন এত উলের ফ্রক, শার্টমাট, সোয়েটার, গেঞ্জি, মোজা পরিয়ে তুলোর হাঁসের মতো সাজিয়ে রাখবার চাল ছিল না। খুব শীত পড়লে একটা জামার উপরে আর একটা সাদা জামা, তার উপরে বড় জোর একটা বনাতের ফতুয়া, এই পর্যন্ত। চীনে বাড়ির জুতে কখনো ক্বচিৎ তৈরি হয়ে আসত—তা সে কোন্ আলমারির চালে পড়ে থাকত খবরই হত না, খেলাতেই মত্ত।
রাত্রে ঘুমোবার আগে দাসীরা আমাদের খানিকটা দুধ খাইয়ে মশারির ভিতরে ঠেলে দিয়ে থাবড়ে থুবড়ে শুইয়ে চলে যেত। তাদেরও আবার নিজেদের একটা দল ছিল। রাত্তিরবেলা দাসীরা সব একসঙ্গে হয়ে, বারান্দায় একটা লম্বা দোলনা ছিল, তাতে বসে গল্পগুজব হাসিতামাসা করত। আন্দিবুড়ি আসত রাত্রে, সে যা চেহারা তার—কপালজোড়া সিঁদুর, লাল টকটক করছে, গোল এত্তো বড় মুখোশের মতো মুখ, যেন আহ্লাদী পুতুলকে কেউ কালি মাখিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। দেখতে যদি তাকে রাত্তিরবেলা! সেই আন্দিবুড়ি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসত মায়েদের শ্যামা-সংগীত শোনাতে, আর পয়সা নিতে। তার গলার স্বর ছিল চমৎকার। সে যখন চাঁদের আলোতে বারান্দার দোলনাতে চুল এলিয়ে বসে দাসীদের সঙ্গে গল্প করত, মশারির ভিতর থেকে ঝাপসা ঝাপসা দেখে মনে হত, যেন সব পেত্নী—গুজ্গুজ্ ফুস্ফুস্ করছে। তখন ওই একটা শব্দ ছিল দাসীদের কথাবার্তার—গুজ্গুজ্, ফুস্ফুস্। বেশ একটু স্পষ্ট স্পষ্ট কানে আসত। ঘুমই হত না। মাঝে মাঝে আমি কুঁই কুঁই করে উঠি, পদ্মদাসী ছুটে এসে মশারি তুলে মুখে একটা গুড় নারকেলের নাড়ু, তাদের নিজেদের খাবার জন্যেই করে রাখত, সেই একটি নাড়ু মুখে গুঁজে দেয়; বলে, ‘ঘুমো।’ নারকেল-নাড়ুটি চুষতে থাকি। পদ্মদাসী গুন গুন করে ছড়া কাটে আর পিঠ চাপড়ায়; এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ি। তার পরে এক ঘুমে রাত কাবার। তুমি তো অন্ধকার রাত্রে রাস্তায় ভূতের ভয় পাও; আমার পদ্মদাসী আর আন্দিবুড়িকে দেখলে তবে কি করতে জানিনে। দুজনের ঠিক এক চেহারা। আদিবুড়ি ছিল কালো রঙের আহ্লাদী পুতুল, আর আমার পদ্মদাসী ছিল যেন আগুনে ঝলসানো পদ্মফুল।
ভালো লাগত আমার দুজনকেই। তাই তাদের কথা এখনও মনে পড়ে। সেই আমাকে মানুষ করা পদ্মদাসীর শেষ কি হল শোনো। একদিন সকালে দাঁড়িয়ে আছি তেতলার সিড়ির রেলিং ধরে; সিঁড়ি বেয়ে তখনও নামতে পারিনে দোতলায়। আমি দাঁড়িয়ে দেখছি তো দেখছিই। মস্ত বড় সিঁড়ির ধাপ ঘুরে ঘুরে নেমে গেছে অন্ধকার পাতালের দিকে। এমন সময়ে শুনি লেগেছে ঝুটােপুটি ঝগড়া পদ্মদাসীতে আর মা’র রসদাসীতে দোতলার সিঁড়ির চাতালে। এই হতে হতে দেখি রসদাসী আমার পদ্মদাসীর চুলের মুঠি ধরে দিলে দেয়ালে মাথাটা ঠুকে। ফটাস করে একটা শব্দ শুনলুম। তার পরেই দেখি পদ্মাসীর মাথা মুখ বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। এই দেখেই আমার চিৎকার, ‘আমার দাসীকে মেরে ফেললে, মেরে ফেললে।’ পদ্মদাসী আমার কান্না শুনে মুখ তুলে তাকালে। আলুথালু চুল, রক্তমুখী চেহারা, চোখ দুটাে কড়ির মতে সাদা। তার পর কি হল মনে নেই। খানিক পরে পদ্মদাসী এল, মাথায় পটি বাঁধা। আমায় কোলে নিয়ে দুধ খাইয়ে দিয়ে চলে গেল। সেই যে আমার কাছ থেকে গেল আর এল না। শুনলুম দেশে গেছে।
তখন গরমি কালটা অনেকেই গঙ্গার ধারে বাগানবাড়িতে গিয়ে কাটাতেন। কোন্নগরের বাগানে বাবামশায় যাবেন, ঠিক হল। মা পিসিমা সবাই যাবেন; সঙ্গে যাব আমি আর সমরদা। দাদা থাকবেন বাড়িতে; বড় হয়েছেন, স্কুলে যান রোজ, বাগানে গেলে পড়াশুনোর ক্ষতি হবে। আমার আনন্দ দেখে কে। কাল সকালবেলায় যাব, কিন্তু রাত পোহায় না। ঘুমোব কি! সারারাত ধরে ভাবছি, কখন ভোর হয়।
বাবামশায় ওঠেন রোজ ভোর চারটের সময়ে। উঠে হাতমুখ ধুয়ে সিঁড়ির উপরে ঘড়ির ঘরে বসে কালীসিংহের মহাভারত পড়েন, সঙ্গে থাকেন ঈশ্বরবাবু। ওই একটি সময়ে আমরা বাবামশায়ের কাছে যেতে পেতুম। চাকররা আমাদের ভোর না হতে তুলে হাতমুখ ধুইয়ে নিয়ে আসত বাবামশায়ের কাছে। তিনি পড়তেন, আমাদের শুনতে হত। এই গল্প শোনা দিয়ে শিক্ষা শুরু করেছি তখন। কোনো-কোনোদিন ভালো লাগে গল্প শুনতে, কোনোদিন ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে। মাঝে মাঝে বাবামশায় খানিকটা পড়ে সমরদাকে পড়তে দেন। বলেন, ‘নাও, এবার তুমি পড়ো।’ সমরদা সেই মস্ত মোটা মহাভারতের বই হাতে নিয়ে বেশ গড় গড় করে পড়ে যান। আমাকে কিন্তু বাবামশায় কোনোদিন বলতেন না পড়তে। বললে কি মুশকিলেই পড়তুম তখন বলো তো! এখন কোন্নগরে তো যাওয়া হবে—কত দেরি করেছিল সেদিন সকালটা আসতে। যেমন রামলাল ডাকা ‘ওঠো’, অমনি তড়িঘড়ি বিছানা থেকে লাফিয়ে পড়ে তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে ইজের কামিজ বদলে তৈরি হয়ে নিলুম। লোকজন আগেই চলে গেছে বাগানে। এবার আমরা যাব। সাদা জুড়িঘোড়া জোতা মস্ত ফিটন দাঁড়াল দেউড়িতে ভোর পাঁচটায়। আমরা উঠলুম তাতে।
বাবামশায় বসলেন পিছনের সিটে, আমাদের বসিয়ে দিলেন সামনেরটায়। দুপাশে বসলেন আরও দুজন, পাছে আমরা পড়ে যাই। সেকালের গাড়িগুলির দু-পাশ থাকত খোলা—একটুতেই পড়ে যাবার সম্ভাবনা। মা পিসিমা আগেই রওনা হয়েছেন বন্ধ আপিসগাড়িতে। আমাদের ফিটনের পিছনে দুই দুই সহিস হাঁকছে পঁইস, পঁইস; ঘোড়া পা ফেলছে টগ্বগ্ টগ্বগ্। গাড়ি চলতে লাগল জোড়াসাঁকোর গলির মোড়ে শিবমন্দির পেরিয়ে। বড় রাস্তার তেলের আলোগুলি তখনও জ্বলছে, চারদিক আবছা অন্ধকার। ঘুমন্ত শহরের মধ্যে দিয়ে গঙ্গার উপরে হাওড়ার পুলের মুখে এলুম। দূর থেকে দেখি পুলের উপরে উঁচু দুটো প্রকাণ্ড লোহার চাকা, তার আদ্ধেক দেখা যাচ্ছে। হাওড়ার পুল দেখি সেই প্রথম, আমি তো ভয়ে মরি। ওই চাকা দুটোর উপর দিয়েই গাড়ি যাবে নাকি? যদি গাড়ি পড়ে যায় গড়িয়ে গঙ্গায়? যতই গাড়ি এগোয় ততই ভয়ে দু-হাতে গাড়ির গদি শক্ত করে ধরে আঁটসাঁট হয়ে বসি, শেষে দেখি গাড়ি ওই চাকা দুটোর মাঝখান দিয়ে চলে গেল। চাকা দুটোর মাঝখানে যে অমনি সোজা রাস্ত আছে গাড়ি যাবার, তা ভাবতেই পারিনি আমি তখন। হাওড়ার পুলের অপর মুখে টোলঘর পেরিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলুম, বড় বড় গাছের নিচে দিয়ে, গাঁয়ের ভিতর দিয়ে—গাঁগুলি তখনো জাগেনি ভালো করে, মাকড়শার জালের মতো ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তার মাঝ দিয়ে চলেছি আমরা। কখনও বা থেকে থেকে দেখা যায় গঙ্গার একটুখানি; ভাবি, এই বুঝি এসে গেলুম বাগানে। আবার বাঁক ঘুরতেই গঙ্গা ঢাকা পড়ে গাছের ঝোপে। শালকের কাছাকাছি এসে কি সুন্দর পোড়া মাটির গন্ধ পেলুম। এখনও মনে পড়ে কি ভালো লেগেছিল সেই সোঁদা গন্ধ। সেদিন গেলুম ওই রাস্তা দিয়েই বালিতে; কিন্তু সেই চমৎকার পল্লীগ্রামের সৌগন্ধ্য পেলুম না। সেই শালকে চিনতেই পারলুম না। শহর যেন পাড়াগাঁকে চেপে মেরেছে। আশেপাশে গলিঘুঁজি, নর্দমা। মাঝরাস্তায় ঘোড়া বদল করে আবার অনেকক্ষণ ধরে চলতে চলতে পৌঁছলুম সবাই কোন্নগরের বাগানে। তখন মোটরগাড়ি ছিল না যে এক ঘণ্টায় পৌছে দেবে শহর থেকে বাগানে। সে ভালো ছিল, ধীরে ধীরে কত কি দেখতে দেখতে যেতুম। গাঁয়ের মেয়েরা পুকুরঘাটে গা ধুতে নেমেছে, পাঠশালায় চলেছে ছেলেরা সরু সরু লাল রাস্তা বেয়ে, মাঝে মাঝে এক-একখানা হাটুরে গাড়ি চলে যাচ্ছে আমাদের গাড়ি বাঁচিয়ে শহরের দিকে। কোনো এক বুড়োমানুষ ঘরের দাওয়ায় উবু হয়ে হুঁকো টানছে। মুদির দোকানে মুদি ঝাঁপ তুলছে। বাঁশঝাড়ে সকালের আলো ঝিলমিল করছে; একটি দুটি দাঁড়কাক ডাকছে সেখানে। রথতলার রথটা খাড়া রয়েছে। এমনি কত কি সুন্দর সুন্দর দৃশ্য! হঠাৎ দেখা দিল ধানখেতের প্রকাণ্ড সবুজ, তার পরই কোতরঙের ইঁটখোলা—সেখানে পাহাড়ের মতো ইঁটের পাজায় আগুন ধরিয়েছে, তা থেকে ধোঁয়া উঠছে আস্তে আস্তে আকাশে। তার পরই কোন্নগরের বাগান আমাদের। দু-থাক ঢালুর উপরে সাদা ছোট্ট বাড়িখানি। উত্তর দিকে মস্ত ছাতার মতো নিচু একটি কাঁঠালগাছ। বাগানবাড়ির সামনে দাড়িয়ে বুড়ো চাটুজ্জেমশাই—সাদা লম্বা পাকা দাড়ি, মাথায় ঝুঁটি বাঁধা, হাতে একটি গেটেবাঁশের লাঠি, ধবধবে গায়ের রঙ, যেন মুনিঋষি। আমাদের কোলে করে গাড়ি থেকে নামিয়ে নিলেন।
গঙ্গার পশ্চিম পারে আমাদের কোন্নগরের বাগান, ওপারে পেনিটির বাগান, জ্যোতিকাকা মশায় সেখানে আছেন। কোনোদিন এপার থেকে বাবামশায়ের পানসি যায়, কোনোদিন বা ওপার থেকে জ্যোতিকাকামশায়ের পানসি আসে; এমনি যাওয়া আসা। বন্দুকের আওয়াজ করে সিগ্নেলে কথা বলতেন তাঁরা। একবার আমায় দাড় করিয়ে আমার কাঁধের উপর বন্দুক রেখে বাবামশায় বন্দুক ছোঁড়েন, পেনিটির বাগান থেকে ওপারে। জ্যোতিকাকামশায় বন্দুকের আওয়াজে তার সাড়া দেন। কানের কাছে বন্দুকের গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ—গুলি চলে যায় কানের পাশ দিয়ে, চোখ বুজে শক্ত হয়ে দাড়িয়ে থাকি। বাবামশায়ের ভয়ে টুঁ শব্দটি করিনে। আসলে আমায় সাহসী করে তোলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য; কিন্তু তা হতে পেল না।
বাবামশায়ের সাঁতারেও খুব আনন্দ। সাঁতরে তিনি গঙ্গা পার হতেন। আমাকেও সাঁতার শেখাবেন; চাকরদের হুকুম দিলেন, তারা আমার কোমরে গামছা বেঁধে জলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেয়। সাঁতার দেব কি, ভয়েই অস্থির। কোনো রকম করে আঁচড়ে পাঁচড়ে পারে উঠে পড়ি।
একটি ভারি সুন্দর ছোট্ট টাটুঘোড়ার গাড়ি। সেটি ছিল ছোটলাট সাহেবের মেমের; নিলামে কিনেছিলেন বাবামশায়। সে কি আমাদের জন্যে? মোটেও তা নয়। কিনেছিলেন মেয়েদের জন্যে; সুনয়নী বিনয়িনী গাড়িতে চড়ে বেড়াবে। কোন্নগরে সেই গাড়িও যেত আমাদের জন্যে। ছোট্ট টাটুঘোড়ার গাড়িতে চড়ে আমরা রোজ সকালে বেড়াতে যাই। বাগানের বাইরেই কুমোরবাড়ি—চাকা ঘুরছে, সঙ্গে সঙ্গে খুরি গেলাস তৈরি হচ্ছে। ভারি মজা লাগত দেখতে; ইচ্ছে হত, ওদের মতো চাকা ঘুরিয়ে অমনি খুরি গেলাস তৈরি করি। মাঝে মাঝে বড় জুড়িঘোড়া হাঁকিয়ে আসেন উত্তরপাড়ার রাজা। আমার টাটুঘোড়া ভয়ে চোখ বুজে রাস্তার পাশে এসে দাঁড়ায়। জুড়িগাড়ির ভিতরে বসে বৃদ্ধ ডেকে জিজ্ঞেস করেন, ‘কার গাড়ি যায়? কার ছেলে এরা?’ চোখে ভালো দেখতে পেতেন না। সঙ্গে যারা থাকে তারা বলে দেয় পরিচয়। শুনে তিনি বলেন, ‘ও, আচ্ছা আচ্ছা, বেশ, এসেছ তা হলে এখানে। বোলো একদিন যাব আমি।’ তাঁর জুড়িঘোড়া টগবগ করতে করতে তীরের মতো পাশ কাটিয়ে চলে যায়—আমার ছোট্ট টাটুঘোড়া তার দাপটের পাশে খাটো হয়ে পড়ে। দেখে রাস্তার লোক হাসে। যেমন ছোট্ট বাবু তেমনি ছোট্ট গাড়ি, ছোট্ট ঘোড়াটি—সহিসটি খালি বড় ছিল, আর সঙ্গের রামলাল চাকরটি।
কোন্নগরে কী আনন্দেই কাটাতুম। সেখানে কুলগাছ থেকে রেশমি গুটি জোগাড় করে বেড়াতুম দুপুরবেলা। প্রজাপতির পায়ে সুতো বেঁধে ওড়াতুম ঘুড়ির মতো। সন্ধ্যেবেলা বাবামশায়, মা, সবাই ঢালুর উপরে একটি চাতাল ছিল, তাতে বসতেন। আমরা বাগানবাড়ির বারান্দার সিঁড়ির ধাপে বসে থাকতুম গঙ্গার দিকে চেয়ে—সামনেই গঙ্গা। ঠিক ওপারটিতে একটি বাঁধানো ঘাট; তিনটি লাল রঙের দরজা-দেওয়া একতলা একটি পাকা ঘর। চোখের উপর স্পষ্ট ছবি ভাসছে; এখনও ঠিক তেমনিটিই এঁকে দেখাতে পারি। চেয়ে থাকি সেই ঘাটের দিকে। লোকেরা চান করতে আসে; কখনও বা একটি দুটি মেয়ের মুখ দরজা খুলে উঁকি মারে, আবার মুখ সরিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়। আর দেখি তর্তর্ করে গঙ্গা বয়ে চলেছে। নৌকো চলেছে পর পর—কোনোটা পাল তুলে, কোনোটা ধীরে, কোনোটা বা জোরে হু-হু করে। যেদিন গঙ্গার উপরে মেঘ করত দেখতে দেখতে আধখানা গঙ্গা কালো হয়ে যেত, আধখানা গঙ্গা সাদা ধবধব করত; সে কি যে শোভা! জেলেডিঙিগুলো সব তাড়াতাড়ি ঘাটে এসে লাগত ঝড় ওঠবার লক্ষণ দেখে। গঙ্গা হয়ে যেত খালি। যেন একখানা কালো সাদা কাপড় বিছানো রয়েছে। এই গঙ্গার দৃশ্য বড় চমৎকার লাগত। গঙ্গার আর এক দৃশ্য, সে স্নানযাত্রার দিনে। দলের পর দল নৌকো বজরা, তাতে কত লোক গান গাইতে গাইতে, হল্লা করতে করতে চলেছে। ভিতরে ঝাড়লণ্ঠন জ্বলছে; তার আলো পড়েছে রাতের কালো জলে। রাত জেগে খড়খড়ি টেনে দেখতুম, ঠিক যেন একখানি চলন্ত ছবি।
এমনি করে চলত আমার চোখের দেখা সারাদিন ধরে। রাত্রে যখন বিছানায় যেতুম তখনও চলত আমার কল্পনা। নানারকম কল্পনায় ডুবে থাকত মন; স্পষ্ট যেন দেখতে পেতুম সব চোখের সামনে। খড়খড়ির সামনে ছিল কঁঠালগাছ। জ্যোৎস্না রাত্তির, চাদের আলোয় কাঁঠালতলায় ছায়া পড়েছে ঘন অন্ধকার। দিনের বেলায় চাটুজ্যে মশায় বলেছিলেন, আজ রাত্তিরে কাঁঠালতলায় কাঠবেড়ালির বিয়ে হবে। রাত জেগে দেখছি চেয়ে, কাঁঠালতলায় যেন সত্যি কাঠবেড়ালির বিয়ে হচ্ছে, খুদে খুদে আলোর মশাল জ্বালিয়ে এল তাদের বরযাত্রী বরকে নিয়ে, মহা হৈ-চৈ, বাদ্যভাণ্ড, দৌড়োদৌড়ি, হুলুস্থুলু ব্যাপার। সব দেখছি কল্পনায়। কাঁঠালতলায় যে জোনাকি পোকা জ্বলছে তা তখন জ্ঞান নেই।
সেই সেবার কোন্নগরে আমি কুঁড়েঘর আঁকতে শিখি। তখন একটু আধটু পেনসিল নিয়ে নাড়াচাড়া করি, এটা ওটা দাগি। বাগান থেকে দেখা যেত কয়েকটি কুঁড়েঘর। কুঁড়েঘরের চালটা যে গোল হয়ে নেমে এসেছে, তা তখনই লক্ষ্য করি। এর আগে আঁকতুম কুঁড়েঘর—বিলিতি ড্রইং-বইএ যেমন কুঁড়েঘর আঁকে। দাদাদের কাছে শিখেছিলুম এক সময়ে। বাংলাদেশের কুঁড়েঘর কেমন তা সেইবারই জানলুম, আর এ পর্যন্ত ভুল হল না।
কোন্নগরে কতরকম লোক আসত। এক নাপিত ছিল, সে পোষা কাঠবেড়ালির ছানা এনে দিত; খালি বাবুইয়ের বাসা জোগাড় করে এনে দিত। কোনোদিন বহুরূপী এসে নাচ দেখাত। কত মজা। কিছু কিছু পড়াশুনোও করতে হত, শুধু খেলা নয়। গোকুলবাবু পড়া নিতেন আমাদের, বাংলার ইতিহাস মুখস্থ করাতেন। টেবিলের উপরে একটি কাচের গেলাসে আফিমের বড়ি ভিজছে, জলটা লাল হয়ে উঠেছে; ওদিকে মা, ওঁরা বারান্দার বাইরে ছোট চালাঘরে রান্না করছেন। বাবামশায়রা কাঁঠালতলায় গল্পগুজব করছেন, চৌকি পেতে বসে। আমরা মুখস্থ করছি বাংলার ইতিহাসে সিরাজদৌল্লার আমল। একদিন রীতিমত প্রশ্ন লিখে বাবামশায়ের সামনে আমাদের পরীক্ষা দিতে হল; সেই পরীক্ষায় জানো আমি ফার্স্ট প্রাইজ পেয়ে গিয়েছিলুম সমরদাকে টেক্কা দিয়ে, চালাকি নয়। পেয়েছিলুম মস্ত একটা বিলিতি অর্গ্যান বাজনা, এখনও তা আছে আমার কাছে। গানও শিখেছিলুম তখন একটি ওই বুড়ো চাটুজ্যেমশায়ের কাছে।
হায় রে সাহেব বেলাকর
আমি গাই দেব তুই বাছুর ধর্।
ওটি শিষ্ট বাছুর, গুঁতোয় নাকো
কান দুটো ওর মুচড়ে ধর্।
হায় রে সাহেব বেলাকর॥
এই আমার প্রথম গান শেখা। ব্লাকইয়র সাহেব রোজ ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়ে ফেরবার সময় গয়লাবাড়ি গিয়ে গয়লানীর কাছে এক পো করে দুধ খেতেন পাড়ার লোকে এই দেখে তার নামে গান বেঁধেছিল।
০৫. জোড়াসাঁকোর দুটো স্বতন্ত্র বাড়ি
জোড়াসাঁকোর দুটো স্বতন্ত্র বাড়িই তো এখন দেখছ? আসল জোড়াসাঁকোর বাড়িই এবার বুঝে দেখো। সে ছেলেবেলার জোড়াসাঁকোর বাড়ি তো আর নেই। দুটো বাড়ির একটা তো লোপাট হয়ে গেছে, একটা আছে পড়ে। আগে ছিল দু-বাড়ি মিলিয়ে এক বাড়ি, এক বাগান, এক পুকুর, এক পাঁচিলে ঘেরা, এক ফটক প্রবেশের, এক ফটক বাইরে যাবার। যেমন এই উত্তরায়ণ, এক ফটক—ভিতরে উদয়ন, কোণার্ক, শ্যামলী, পুনশ্চ, উদীচী, সব মিলিয়ে এক বাড়ি, জোড়াসাঁকোর বাড়িও ছিল তেমনি। এক কর্তা দ্বারকানাথ, তার পর দেবেন্দ্রনাথ, তার পর রবীন্দ্রনাথ— এই তিন কর্তা পর পর।
অনেকগুলো ঘর, অনেকগুলো মহল, অনেকখানি বাগান জুড়ে দুই বাড়ি মিলিয়ে এক বাড়ি ছিল ছেলেবেলার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। এ-বাড়ি ও-বাড়ি বলতুম মুখে, কিন্তু ছেলেবুড়ো চাকরবাকর সবাই জানতুম মনে দুখান বাড়ি এক বাড়ি। কারণ, এক কর্তা ছিল; একই নম্বর ছিল, ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি। একই ফটক ছিল প্রস্থান-প্রবেশের। সেই একই তাল ভাঙা লোহার খোলা ফটক; তার একধারে একটি বুড়ো নিমগাছ, তার কোটরে কোটরে পাপদুয়া, টুনটুনি পাখিদের বাসা; আর একধারে একটি মাত্র গোলকচাঁপার গাছ, আগায় ফুল, গোড়ায় ফুল ফুটিয়ে। এই ফটককে শ্যাম মিস্ত্রি মাঘোৎসবের দিনে লোহার কিরীট পরাত; তাতে আলোর শিখায় জ্বলত ‘একমেবাদ্বিতীয়ম্’। জোড়াসাঁকো নাম ছিল বাড়ির, দুটাে বাড়িও ছিল বটে, কিন্তু ওই দুই সাঁকোর তলা দিয়ে যে এক নদীর স্রোত বইত; সেদিন আর নেই, সে বাড়িও আর নেই।
এক ঘণ্টা পড়ত ও-বাড়িতে সকাল ছটায়; এ-বাড়িতে উঠতুম সেই শব্দ শুনে চাকর-দাসী, ছেলে-মেয়ে, মনিব, সবাই। সাতটার ঘণ্টা পড়ত, তখন যে যার কাজে লাগতুম। এমনি নটা দশটা সাড়ে দশটা বাজল, কাছারি খুলল, আমরা খেয়েদেয়ে স্কুলে গেলুম। তারপর আবার ঘণ্টা পড়ত বেলা তিনটেয়। স্কুলের গাড়ি ফিরত, বৈকালিক জলযোগের ব্যবস্থা হত, হাওয়া খেতে যাবার জন্যে গাড়ি জোড়া হত, আমরা খেলা জুড়তুম বাগানে ছুটােছুটি। এমনি চলত নটা পর্যন্ত। ঐ এক ঘন্টার শব্দ দুটাে বাড়ির সব লোককে যেন চালাচ্ছে। রাত নটায় ঘন্টা বাজত নিদ্রার সময় এল এই কথা জানিয়ে। এই ছিল তখন। তুমি কি ভাবছ সামান্ত বাড়ি ছিল? হারিয়ে যাবার ভয় হত এঘর ও-ঘর ঘুরে আসতে। তখনকার দিনে মহল ভাগ করে বাস করার প্রথা ছিল। মোটামুটি বড় ভাগ ছিল অন্দরমহল আর বারমহল; তার ভিতরে আবার ছোট ছোট ভাগ—রান্নাবাড়ি, গোলাবাড়ি, পুজোবাড়ি, গোয়ালবাড়ি, আস্তাবলবাড়ি, এমনি কত বাড়ি। তার মধ্যে আবার কত ঘর ভাগ—ভিস্তিখানা, তোশাখানা, বাবুর্চিখানা, নহবতখানা, দপ্তরখানা, কাছারিখানা, গাড়িখানা, স্কুলঘর, নাচঘর, দূরদালান, দেউড়ি; যেন অনেক খানাখন্দ নিয়ে একটা তল্লাট জুড়ে একখানা ব্যাপার।
তেতলায় অন্দর-মহল, দোতলায় বারান্দা। একতলার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে দপ্তরখানা, দক্ষিণ-পুব দিকে ছোট পিসেমশায়ের আপিসঘর। তিনি লম্বা একটা খাতায় ডায়েরি লিখেই যাচ্ছেন—পাশে গিয়ে দাঁড়াই, একবার তাকিয়ে আবার লেখায় মন দেন। বলেন, ‘কি, এসেছিস ? আচ্ছা।’ বলে একমুঠো পাতলা পাতলা লজেঞ্জুসের মতো ওয়েফার হাতে দিয়ে বিদেয় করেন, বলেন, ‘দেখিস খাসনে যেন।’
মাঝখানে যে বড় হলঘরটা সেটা তোশাখানা। তোশাখানা চাকরদের আড্ডাঘর। বাবামশায়ের গোবিন্দ চাকর তোশাখানার সর্দার। অন্য চাকররা তাকে ভয় করে চলে। দাদার গদাধর চাকর—এমন বজ্জাত সে, তাকে যা ভয় করি সবাই! দারুণ প্রহার করে আমাদের। চেহারাও তেমনি, নৰ্ম্যাল স্কুলের লক্ষ্মীনারায়ণ পণ্ডিতের মত ভীষণ। বাড়ির পুরানো চাকর। একবার দেশে গেল আর ফিরে এল না। কি হল গদার, সে আসছে না কেন? গদা বলেই ডাকত সবাই তাকে। শোনা গেল মারা গেছে সে; বুড়ো হয়েছিল, মাঠেই মরে পড়ে ছিল, শেয়াল তাকে খেয়ে সাফ করে ফেলেছে। শিশুমন, তার দৌরাত্মিতেই অস্থির ছিল সারাক্ষণ, মনে মনে ভাবলুম, বেশ হয়েছে, যেমন আমাদের মারত, আপদ গেছে।
সমরদার চাকর দুর্গাদাস; আমার রামলাল, ভালোমানুষ সে। পদ্মদাসী চলে যেতে রামলাল বহাল হয় আমার কাজে। রমানাথ ঠাকুরের খাস চাকর ছিল আগে। তিনি চাকর রাখতেন নরম হাত দেখে। গায়ে তেল মাখাতেন বোধ হয়; কড়া হাত গায়ে লাগলেই ধমকে উঠতেন, ‘যাঃ যাঃ, এ যেন গায়ে খড়রা মাজছে।’ রামলালের হাত ছিল নরম। কি কারণে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন জানিনে; বোধ হয় দেশে গিয়ে ফিরতে দেরি করেছিল। যা হোক আমি তো পড়লুম তার চার্জে। সব ছেলেদের একটি করে চাকর থাকে। তারাই যেন মাস্টার। আদবকায়দা শেখায়, চোখে চোখে রাখে। কারণ, ছেলেরা কিছু করলে দোষ চাকরদেরই। চাকরদের কাছেই জিম্মে থাকে ছেলেদের এক-একজনের এক-একটি আলমারি, তাতে যার যার কাপড়জামা, থালাবাসন, ব্যবহারের যাবতীয় বস্তু। চাবিও থাকে চাকরদের কাছেই। দরকারমত বের করে দেয়, আবার ধুয়ে মুছে সাফ করে তুলে রাখে। দুধ খাবার বাটিও থাকে বাড়ির ভিতরে দাসীর কাছে।
তোশাখানা শুধু চাকরদের থাকবার জন্যে, বেয়ারারা থাকে অন্যদিকে। ঘরের উত্তরে দক্ষিণে দু-দিকে দু-সারি আলমারি কাপড়ে বাসনে বোঝাই। পুবে পশ্চিমে কয়েকখানা বড় বড় তক্তা পাতা, তক্তার মাঝখানে একটি করে বাক্স বসানো। ডালা খুলে দেখি, তাদের খেলার দাবার ছক, তাস, আয়না, চিরুনি, এই সব নানা জিনিসপত্রে ভরা। সেই তক্তার উপরেই মাদুর বালিশ বিছিয়ে তারা ঘুমোয়। আবার কোনো কোনো দিন দেখি, বাবামশায়দের বৈঠক ভাঙলে তারা ফিটফাট বাবু সেজে রুপোর ট্রেতে করে সোডা লেমনেড খায়, রুপোর পেয়ালায় চা পান করে। বাবুদের আড্ডা ভাঙলে তাদের আড্ডা শুরু হয়।
সে-বয়সে চাকরদের তোশাখানায় যখন-তখনই যেতে পারি, সেখানে যাবার আমার ফ্রী লাইসেন্স, কেউ বারণ করে না। রামলাল বলে, ‘এসেছ? আচ্ছা, থাকো এখানেই।’ তাদেরই তেলচিটচিটে বালিশ মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়ি। পাশে রামলাল বসে বাবামশায়ের ধুতি পাট করে দেয় দেখি, দেখতে দেখতে ধুতি চুনোট করে যখন ছেড়ে দেয় ফুলের মত ছড়িয়ে পড়ে।
তোশাখানার পাশে উত্তর দিকটায় ভিস্তিখানা। চানের ঘরে যেতে হয় । ভিস্তিখানার ভিতর দিয়ে, বড় হয়েছি, সাতে পড়েছি; এখন তো আর বারান্দায় বসে হাতমুখ ধুলে চলবে না। চাকর তরিবত শেখাচ্ছে। সকালে উঠে চানের ঘরে গিয়ে হাতমুখ ধোয়া অভ্যেস করতে হচ্ছে। একটিই চানের ঘর নিচে। দাদারা ঢুকছেন এক এক করে। তাদের শেষ না হলে তো আর আমি ঢুকতে পারিনে। অপেক্ষা করছি ভিস্তিখানায়। খুব ভোরেই উঠতে হয় আমাদের। বসে বসে দেখছি।
বিশ্বেশ্বর হুঁকোবরদার, কোন্ রাত থাকতে ওঠে সে। বাবামশায়ের বুদ্ধু বেয়ারা আর বিশ্বেশ্বর এই দুজনে ওঠে সকলের আগে। বাবামশায়ের ছিল খুব ভোরে ওঠা অভ্যেস। বলেছি তো তিনি কত ভোরে উঠে হাতমুখ ধুয়ে রামায়ণ পড়তে বসতেন। বুদ্ধু উঠে বাবামশায়ের ঘর খুলে দিত, বিশ্বেশ্বর ফরসি সাজিয়ে নিয়ে উপস্থিত করত। তা সেই ভিস্তিখানায় বসে দেখছি, একপাশে দ্বারকানাথ ঠাকুরের আমলের পুরোনো একটা টেবিল, খানকয়েক ভাঙা চেয়ার। টেবিলের উপরে বিসুবিয়াসের একটা ছবি, দাউদাউ করে আগুন উঠছে মুখ দিয়ে। তামাক সাজবার ঘর, আগুনের ছবি থাকবে সেখানে। পুরোনো কালের ভালো অয়েলপেন্টিং। অত ভালো অয়েলপেন্টিং ও-রকম করে ফেলে রেখেছিল, তখন অতটা মূল্য বুঝিনি। তা বিশ্বেশ্বর তো সেই টেবিলের উপরে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে সারি সারি ফরসি সাজিয়ে। দিনরাত সে ওই ভিস্তিখানাতেই থাকে, সময় মত তামাক বদলে বদলে দেয়। তার কাজই তাই ।
এই বিশ্বেশ্বরই আমাদের তামাক খেতে শিখিয়েছে; বড় হয়েছি—বিশ্বেশ্বর গিয়ে মার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে এল। বললে, ‘বাবুরা বড় হয়েছেন তামাক না খেলে চলবে কেন?’ মা বললেন, ‘তা ওরা খেতে চায় তো খাওয়া?’ বাড়ির বাবুরা তামাক না খেলে তারও যে চাকরি থাকে না। নানারকম করে সেজে আমাদের তামাক অভ্যেস ধরিয়েছে, প্রথম দিন তো একবার নল টেনেই কেশে মরি। সে আবার শেখায় এ-রকম করে আস্তে আস্তে টানুন। অমন ভড়াক করে টানলে তো কাশি উঠবেই।
তা ওই ভিস্তিখানাও ছিল একটা দস্তুরমত আড্ডার জায়গা। মণিখুড়ো, নিরুদাদা, ঈশ্বরবাবু, বাড়ির বড় ছেলেরা যারা তামাক খাওয়া সবে শিখছেন সকলেই ঘুরে ফিরে আসতেন সেখানে। ঈশ্বরবাবু প্রতিদিন সকালে বাবামশায়ের কাছে বসে রামায়ণ পড়া শোনেন। রামায়ণ শেষ হয়ে গেলে বুড়ো একটি লাঠি হাতে নিয়ে ঠকাস ঠকাস করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসেন নিচে ভিস্তিখানায়। এসেই একটা ভাঙা চৌকিতে বসে বলেন, ‘বিশ্বেশ্বর।’ বিশ্বেশ্বরের তৈরিই থাকে সব। ‘এই যে বাবু’ বলে হুঁকোটি হাত বাড়িয়ে ধরলে। ঈশ্বরবাবু তা হাতে নিয়ে ফক্ ফক্ করে কয়েকবার ধুঁয়ো ছেড়ে হুঁকোটি ফিরিয়ে দিয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে তা থেকে একটি পয়সা বিশ্বেশ্বরের হাতে দিয়ে বলেন, ‘এই নাও।’ বিশ্বেশ্বর সেটি পকেটে রাখে। ঈশ্বরবাবু খোঁড়াতে খোঁড়াতে চলে যান বাজারে। সন্ধ্যেবেলা যখন উপরে উঠে আসেন ভিস্তিখানা হয়ে, বিশ্বেশ্বর তখন আবার সেই একটি পয়সা ফেরত দেয় তাঁকে, তিনি তা রুমালে বেঁধে রাখেন। রোজই দেখি, এক পয়সার লেন-দেন চলে ঈশ্বরেতে, বিশ্বেশ্বরেতে, এর মানে কি কে জানে তখন! সকালে ঈশ্বরবাবু চলে গেলে আসেন মণিখুড়ো। ‘কই বাবা বিশ্বেশ্বর, আছে কিছু?’ ‘আজ্ঞে হ্যাঁ হ্যাঁ, নিন না, এখনও আছে এতে।’ বলে ঈশ্বরবাবুর সেই হুঁকোটি তার হাতে তুলে দেয়। তিনি আবার ফক্ ফক্ করে খানিক ধুঁয়ো ছাড়েন।
এই মণিখুড়ো আর বিশ্বেশ্বরে একবার কেমন লেগেছিল শোনো। এখন, সামনে পুজো এসে গেছে, আর বেশি দেরি নেই। মণিখুড়ো বাবামশায়ের কাছে পার্বনী চেয়ে নিয়ে শখ করে বাজার থেকে একজোড়া কালো কুচকুচে বার্নিশকরা জুতো কিনে এনেছেন, পায়ে দিয়ে পুজো দেখতে যাবেন। কাগজে-মোড়া জুতোজোড়া এনে ভিস্তিখানার এক কোণায় গুঁজে রেখে দিলেন—কি জানি চাকরবাকর কেউ যদি সরিয়ে ফেলে, এই ভয়। বিশ্বেশ্বর ঘরেই ছিল, দেখলে ব্যাপারটা—বাবু কি যেন এনে রাখলেন কোণে। মণিখুড়ো তো জুতো রেখে তামাক খেয়ে চলে গেলেন অন্য কাজে। বিশ্বেশ্বর এই ফাঁকে জুতোজোড়া বের করে নিয়ে সেই ঘরেই আর এক কোণে লুকিয়ে রেখে দিলে। এদিকে মণিখুড়ো ফিরে এসে জুতো আর পান না। ঘরের এদিক ওদিক খুঁজে সারা, কোথাও জুতো নেই। বিশ্বেশ্বরকে জিজ্ঞেস করেন, সে বলে, ‘কি জানি বাবু, আমি দেখিনি ওসব। আমি থাকি আমার কাজে ব্যস্ত। তবে কি জানেন, যে আগুন খেয়েছে তাকেই কয়লা ওগরাতে হবে। জুতো যাবে কোথায়?’ মণিখুড়ো বলেন, ‘সে তো বুঝলুম। কিন্তু কে নিলে জুতোজোড়া? শখ করে আনলুম পুজো দেখব বলে।’ বিশ্বেশ্বর সেসব কথায় কানই দেয় না। মণিখুড়ো তাকে তাকে আছেন। পরদিন সকালবেলা বিশ্বেশ্বর রোজকার মতো বাবামশায়ের জন্য তামাক সাজছে; মণিখুড়ো এক কোণায় হুঁকো হাতে বসে। বিশ্বেশ্বর কিসের জন্য যেই না একটু ঘরের বাইরে গেছে, টেবিলের উপর ছিল সারি সারি রুপোর মুখনল সাজানে, মণিখুড়ো তা থেকে বাবামশায়ের মুখনলটা সরিয়ে ফেললেন। বিশ্বেশ্বর ঘরে ঢুকল। মণিখুড়ো ওদিকে বসে হুঁকো হাতে ধোঁয়া ছাড়ছেন আর আড়ে আড়ে এদিকে ওদিকে চাইছেন। বিশ্বেশ্বর তো তামাক সেজে গড়গড়ার নল গোলাপজল দিয়ে, কাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সাফ ক’রে, মুখনল পরাতে যাবে, মুখনল নেই। কি হবে এখন? বিশ্বেশ্বরের চক্ষুস্থির। কে নিলে বাবুর ফরসির মুখনল! অস্থির হয়, খুঁজে বেড়াতে লাগল। এদিকে বাবামশায়ের তামাক খাবার সময় হয়ে এসেছে। ঠিক সময়ে তামাক দিতে না পারলে মহামুশকিল। মণিখুড়োকে জিজ্ঞেস করে; তিনি বলেন, ‘কই বাবা, দেখিনি কিছু। আমি তো এখানে বসে সেই থেকে হুঁকো খাচ্ছি। তবে কি জান, যে আগুন খেয়েছে তাকে কয়লা ওগরাতেই হবে। ভেবে কি করবে। এই দেখনা কাল আমার জুতোজোড়াটি কেমন লোপাট হয়ে গেল। খুঁজে দেখ, পাবে হয়তো—যাবে কোথায়? বিশ্বেশ্বর বললে, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ, তা হলে খুজে দেখি। আপনার জুতোই বা যাবে কোথায়?’ বলে ঘরের এ-কোণায় ও কোণায় খুঁজতে খুঁজতে এক জায়গা থেকে কাগজে-মোড়া জুতো বের করে আনলে; বললে, ‘বাবু, এই যে আপনার জুতো পাওয়া গেছে।’ মণিখুড়ো বললেন, ‘ওই যে ওই কোণায় তোমার মুখনল চকচক করছে।’ বিশ্বেশ্বর তাড়াতাড়ি জুতো ফেরত দিয়ে মুখনল নিয়ে বাঁচে।
দেউড়িতে দরোয়ানদের বৈঠক । মনোহর সিং বুড়ো দরোয়ান—মস্ত লম্বা চওড়া, ফরসা গায়ের রঙ, ধবধব করছে সাদা দাড়ি। সকালে সে একদিকে খালি গায়ে লুঙ্গি প’রে বসে দই দিয়ে দাড়ি মাজে আর চারদিকে অন্য দরোয়ানরা কুস্তি করে, ডাম্বেল ভাঁজে। একপাশে এক দরোয়ান একটা মস্ত গয়েশ্বরী থালাতে একতাল আটার মাঝখানে গর্ত করে তাতে খানিকটা ঘি ঢেলে মাখতে থাকে। সে এক পর্ব সকালবেলায় দেউড়িতে। এদিকে মনোহর সিং দই দিয়ে দাড়িই মাজছে বসে বসে। ঘণ্টাখানেক এইভাবে মেজে বাঁ হাতে ছোট্ট একটি টিনের আয়না মুখের সামনে ধ’রে, একরকম কাঠের চিরুনি থাকত তার ঝুঁটিতে গোঁজা, সেই চিরুনি দিয়ে দাড়ি বেশ করে আঁচড়ে কাপড়জামা পরে কোমরে ফেটি বেঁধে, একপাশে প্রকাণ্ড কাঠের সিন্দুক, তাতে ঠেস দিয়ে দোজানু হয়ে যখন বসে দু উরুতে দু হাত রেখে, কি বলব, ঠিক যেন পাঞ্জাবকেশরী বসে আছে ঢাল-তলোয়ার পাশে নিয়ে। শুভ্রবেশ তার, গলায় মোটা মোটা আমড়ার আঁঠির মতো সোনার কন্ঠি, হাতে বালা, কোমরে গোঁজা বাঁকা ভোজালি, সে ছিল দেউড়ির শোভা। পশমের মতো সাদা লম্বা দাড়ি কি সুন্দর লাগত। ছেলেবুদ্ধি— দেখেই একদিন কি ইচ্ছে হল, হাত দিয়ে ধরে দেখব তা। যেই না মনে হওয়া খপ করে গিয়ে তার দাড়ি চেপে ধরলুম মুঠোর মধ্যে। মনোহর সিং অমনি গর্জন করে কোমরের ভোজালিতে হাত দিলে। আমি তো দে ছুট একেবারে দোতলায়। ভয়ে আর নামিনে একতলায়। প্রাণের ভিতর ধুক্ ধুক্ করছে, কি জানি কি অন্যায় বুঝি করে ফেলেছি। এবার আমায় দরোয়ানজি কেটেই ফেলবে। উঁকিঝুঁকি দিই, মনোহর সিং আমায় দেখতে পেলেই গর্জন করে ওঠে, আর আমার ভয়ে প্রাণ শুকিয়ে যায়। রামলাল আমায় শিখিয়ে দিলে, ‘দাড়িতে হাত দিয়েছ তুমি, ভারি দোষ করেছ। যাও, হাত জোড় করে দরোয়ানজির কাছে ক্ষমা চেয়ে এস। শেষে একদিন দেউড়িতে গিয়ে ভয়ে ভয়ে অতি কাতর ভাবে দু হাত জোড় করে কচলাতে কচলাতে বললুম, ‘এ দরোয়ানজি, মাপ করো আমার কসুর হয়ে গেছে। আর এমন কাজ কখনও করব না।’ মনোহর সিং মিটির মিটির হেসে ভারি গলায় বললে, ‘আর করবে না তো? ঠিক? আচ্ছা যাও।’ মনোহর সিঙের ক্ষমা পেয়ে তবে আমার ত্ৰাস কাটে, দোতলা থেকে নামতে পেরে বাঁচি।
দেউড়িতে মাঝে মাঝে নানারকম মজার কাণ্ড হত। একবার কে একজন এল, সে বাজি রেখে একমণ রসগোল্লা খেতে পারে। ঘোষাল ছিলেন খাইয়ে লোক। তিনি শুনে বললেন, ‘আমিও খাব।’ যে হারবে দশ টাকা দণ্ড দেবে। এ-বাড়ির ও-বাড়ির যত দরোয়ান এসে ভিড় করল দেউড়িতে। আমরাও ছেলেপিলেরা, গাড়িবারান্দায় ছিল সারি সারি গাড়ি সাজানো, কেউ তাতে উঠে, কেউ পাদানিতে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম। মনোহর সিঙের সামনে বসে গিয়েছে দুজন রসগোল্লা খেতে। ওদিকে একপাশে মস্ত কড়াইয়ে হালুইকর এসে চাপালে রস; তাতে গরম গরম রসগোল্লা তৈরি হতে লেগেছে। একজন সামনে তাদের পাতে সেই রসগোল্লা তুলে দিচ্ছে, অন্যরা গুনছে। ঘোষাল খেয়েই চলেছেন। যত রসগোল্লাই তার পাতে দেওয়া হয় নিরেট ভুঁড়িতে তলিয়ে যায়। খেতে খেতে যখন ষোল গণ্ডা রসগোল্লা খাওয়া হয়েছে তখন ঘোষাল হুপ্ হুপ্ করে হেঁচকি তুলতে লাগলেন। দেওয়ানজি যোগেশদাদা বললেন, ‘আর নয়, ঘোষাল, হেঁচকি তুলে ফেললে তোমারই হার হল। ঘোষাল মশায় হেরে দশ টাকা গুনে দিয়ে উঠে পড়লেন। অন্য লোকটা শেষ অবধি পুরো পরিমাণ রসগোল্লা খেয়ে আধকড়াই রস চুমুক দিয়ে টাকা ট্যাঁকে গুজে চলে গেল।
হোলির দিনে এই দেউড়ি গমগম করত; লালে লাল হয়ে যেত মনোহর সিঙের সাদা দাড়ি পর্যন্ত। ওই একটি দিন তার দাড়িতে হাত দিতে পেতুম আবির মাখাতে গিয়ে। সেদিন আর সে তেড়ে আসত না। একদিকে হত সিদ্ধি গোলা; প্রকাণ্ড পাত্রে কয়েকজন সিদ্ধি ঘুঁটছে তো ঘুঁটছেই। ঢোল বাজছে গামুর গুমুর ‘হোরি হ্যায় হোরি হ্যায়’, আর আবির উড়ছে। দেয়ালে ঝুলোনো থাকত ঢোল, হোরির দু-চারদিন আগে তা নামানো হত। বাবামশায়েরও ছিল একটি সবুজ মখমল দিয়ে মোড়া লালসুতোয় বাঁধা—আগে থেকেই ঢোলে কি সব মাখিয়ে ঢোল তৈরি করে বাবামশায়ের ঢোল যেত বৈঠকখানায়, দরোয়ানদের ঢোল থাকত দেউড়িতেই। হোরির দিন ভোরবেলা থেকে সেই ঢোল গুরুগম্ভীর স্বরে বেজে উঠত; গানও কি সব গাইত, কিন্তু থেকে থেকে ওই ‘হোরি হ্যায় হোরি হ্যায়’ শব্দ উঠত। বেহারাদেরও সেদিন ঢোল বাজত; গান হত ‘খচমচ খচমচ’, যেন চড়াইপাখি কিচির কিচির করছে। আর দরোয়ানদের ছিল মেঘগর্জন; বোঝা যেত যে, হ্যাঁ, রাজপুত-পাহাড়ীদের আভিজাত্য আছে তাতে। নাচও হত দেউড়িতে। কোত্থেকে রাজপুতানী নিয়ে আসত, সে নাচত। বেশ ভদ্ররকমের নাচ। আমরাও দেখতুম। বেহারাদের নাচ হত, পুরুষরাই মেয়ে সেজে নাচত সে কী রকম অদ্ভূত বীভৎস ভঙ্গীর, দু হাত তুলে দু বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ধেই ধেই নাচ আর ওই এক খচমচ খচমচ শব্দ। উড়েরাও নাচত সেদিন দক্ষিণের বাগানে লাঠি খেলতে খেলতে। বেশ লাগত। উড়েদের নাচ আরম্ভ হলেই আমরাও ছুটতুম ‘চিতাবাড়ি’ দেখতে।
দোতলায় বাবামশায়ের বৈঠকখানায়ও হোলির উৎসব হত। সেখানে যাবার হুকুম ছিল না। উঁকিঝুঁকি মারতুম এদিক ওদিক থেকে। আধ হাত উঁচু আবিরের ফরাস। তার উপরে পাতলা কাপড় বিছানো। তলা থেকে লাল আভা ফুটে বের হচ্ছে। বন্ধুবান্ধব এসেছেন অনেক— অক্ষয়বাবু তানপুরা হাতে বসে, শ্যামসুন্দরও আছেন। ঘরে ফুলের ছড়াছড়ি। বাবামশায়ের সামনে গোলাপজলের পিচকারি, কাচের গড়গড়া, তাতে গোলাপজলে গোলাপের পাপড়ি মেশানো, নলে টান দিলেই জলে পাপড়িগুলো ওঠানামা করে। সেবার এক নাচিয়ে এল। ঘরের মাঝখানে নন্দফরাশ এনে রাখলে মস্ত বড় একটি আলোর ডুমটি। নাচিয়ে ডুমটি ঘুরে ঘুরে নেচে গেল। নাচ শেষ হল; পায়ের তলায় একটি আলপনার পদ্ম আঁকা। নাচের তালে তালে পায়ের আঙুল দিয়ে চাদরের নিচের আবির সরিয়ে সরিয়ে পায়ে পায়ে আলপনা কেটে দিলে। অদ্ভুত সে নাচ।
বৈঠকখানা আর দেউড়ির উৎসব, এ দুটাের মধ্যে আমার লাগত ভালো রাজপুত দরোয়ানদের উৎসবটাই। বৈঠকখানায় শখের দোল শৌখিনতার চুড়ন্ত—সেখানে লট্কনে ছোপানো গোলাপী চাদর, আতর, গোলাপ, নাচ, গান, আলো, ফুলের ছড়াছড়ি। কিন্তু সত্যি দোল-উৎসব করত দরোয়ানরাই—উদ্দণ্ড উৎসব, সব লাল, চেনবার জো নেই। সিদ্ধি খেয়ে চোখ দুটো পর্যন্ত সবার লাল। দেখলেই মনে হত হোলিখেলা এদেরই। শখের খেলা নয়। যেন যারা রক্তের হোলি খেলতে জানে, এ তাদেরই খেলা। কৃত্রিম কিছু নেই। দেখলে না সেদিন সাঁওতালদের উৎসব? কৃত্রিমতা ঘেঁষতে পায় না সেখানে। তারা মনের আনন্দে উৎসব করে, আনন্দে নাচে গায়, তাতে তারা মেতে যায়। বৈঠকখানার উৎসব ছিল কৃত্রিম, তাই তা ভালো লাগত না আমার।
দেউড়ি আর বৈঠকখানায় ছিল এইরকম দোল-উৎসব, আর আমাদের জন্য আসত টিনের পিচকারি। ওইতেই আনন্দ। টিনের পিচকারি বালতিভরা লাল জলে ডুবিয়ে যাকে সামনে পাচ্ছি পিচকারি দিয়ে রঙ ছিটিয়ে দিচ্ছি আর তারা চেঁচামেচি করে উঠছে, দেখে আমাদের ফুর্তি কী। বাড়ির ভিতরে সেদিন কি হত জানিনে, তবে আমাদের বয়েসে খেলেছি দোলের দিনে— আবির নিয়ে এ-বাড়ি ও-বাড়ির অন্দরে ঢুকে বড়দের পায়ে দিতুম, ছোটদের মাথায় মাখাতুম। বড়দের রঙ মাখাবার হুকুম ছিল না, তাঁদের ওই পা পর্যন্ত পৌঁছত আমাদের হাত।
এই তো গেল দোলপূর্ণিমার কথা। এখন আর এক কথা শোনো। বাবামশায়ের সমশের কোচোয়ান, আস্তাবলবাড়ির দোতলার নহবতখানায় থাকে। তিনটে বাজলেই সে বেরিয়ে এসে বসে আস্তাবলের ছাদে খাটিয়া পেতে, ফরসি হাতে; ঠিক একটি ফুলদানির মতে ফরসি ছিল তার। আক্কেল সহিস তামাক সেজে ফরসি এনে হাতে দেয়, তবে সে তামাক খায়। সহিসরা ছিল তার চাকর; সব কাজ করে দিত, নিজের হাতে সে কিছু করত না। দূর থেকে দেখছি, সমশের আয়েস করে ফরসি হাতে খাটিয়ায় বসে তামাক খাচ্ছে, আক্কেল সহিস তার বাবরি চুল বাগাচ্ছে, ঘণ্টাখানেক ফাঁপিয়ে ফাঁপিয়ে চুল আঁচড়াবার পর একটি আয়না এনে সামনে ধরলে। সমশের বাদশাহী কায়দায় বাঁ হাতে আয়নাটি ধরে মুখ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে গোঁফ মুচড়ে আয়না ফেরত দিয়ে উঠল। ঘরে গিয়ে চুড়িদার জরিদার বুককাটা কাবা প’রে পা বের ক’রে দিতে আর একজন সহিস শুঁড়তোলা দিল্লীর লপেটা তার পায়ে গুঁজে দিল। আর এক সহিস মাথার শামলাটা দু-হাতে এনে সামনে ধরল, সমশের পাগড়িটা মাথার উপর থাবড়ে বসিয়ে হাতিমার্কা তকমার দিকটা হেলিয়ে উঁচু করে দিলে। অন্য সহিস ততক্ষণে লম্বা চাবুকটা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সমশের চাবুক হাতে নিয়ে এবারে দোতলা থেকে নামল মাটির সিঁড়ি দিয়ে। নিচে ঘোড়া ঠিক করে রেখেছে সহিসরা—দুধের মতো সাদা জুড়ি। সেই জুড়িঘোড়া গাড়িতে জোতবার আগে খানিক ছুটিয়ে ঠিক করে নিতে হত। যেখানে রবিকার লালবাড়ি সে জায়গা জোড়া ছিল গোলচক্কর প্রাচীরঘেরা। একপাশে ছোট্ট একটি ফটক। সহিসরা ঘোড়া দুটাে চক্করে ঢুকিয়ে ফটক বন্ধ করে দিল। সমশের লম্বা চাবুক হাতে প্রাচীরের উপর উঠে দাড়িয়ে বাতাসকে চাবুক বসালে—শট্। সেই শব্দ পেয়ে ঘোড়া দুটো কান খাড়া করে গোল চক্করে চক্কর দিতে শুরু করলে। একবার করে ঘোড়া ঘুরে আসে আর চাবুকের শব্দ হয় শট্ শট্। যেন সার্কাস হচ্ছে। এই রকম আধ ঘণ্টা ঘুরিয়ে সমশের কোচোয়ান চাবুক আক্কেল সহিসের হাতে ছেড়ে দিয়ে নামল। আক্কেল গাড়ি বের করলে—ঝকঝক তকতক করছে গাড়ির ঘোড়ার রুপো-পিতলের শিকলি-সাজ। গাড়িতে জুড়ি জোতা হলে পর সমশের কোচবাক্সে উঠে হাত গুটিয়ে দাঁড়াতেই সহিস রাশ তুলে দিলে তার হাতে। রাশ ধরবার কায়দা কি ছিল সমশের কোচোয়ানের, দশ আঙুলের ভিতরে কেমন কায়দা করে ধরত! সেই রাশে একবার একটু টান দিতেই বড় বড় দুটাে ঘোড়া তড়বড় করে এসে গাড়িবারান্দায় ঢুকল। গাড়িবারান্দায় ঢুকতেই যে পুরু কাঠের পাঠা পাতা থাকত সেটা শব্দ দিলে একবার হুড়ুদুম্ যেন জানান দিলে গাড়ি হাজির। বাবামশায় হাওয়া খাবার জন্য তৈরি হয়ে গাড়িতে চাপলেন। গাড়ি চলল গাড়িবারান্দা ছেড়ে। সমশের তখনও দাঁড়িয়ে রাশ হাতে কোচবাক্সে। কাঠখানা চারখানা চাকার চাপে আর দুবার শব্দ দিলে হুড়ুদুম্ হুড়ুদুম্। ধপাস্ করে এতক্ষণে সমশের কোচোয়ান কোচবাক্সে জাঁকিয়ে বসল যেন সিংহাসনে বসলেন আর এক লক্ষ্ণৌয়ের নবাব।
আমাদের ছিল রামু কোচোয়ান। জাতে হিন্দু, কিন্তু লুঙ্গি পরত সে। কোচোয়ান হলেই লুঙ্গি পরতে হবে, এই সে জানত। ছোট্ট একটি ফিটন গাড়ি, আমরা তাতে চড়ে বিকেলে চক্করে ঘুরে বেড়াতুম—হাওয়া খাওয়া হয়ে যেত। বেশির ভাগ সুনয়নী বিনয়িনী চড়ত সেই গাড়িতে।
আস্তাবলে কতরকম দৃশ্য দেখবার ছিল—কত লোকের, এ-বাবুর, ও-বাবুর, গাড়ি-ঘোড়া থাকত সেখানে। বেচারামবাবু আসতেন বঁড়শে বেহালা থেকে বুধবারে বুধবারে দাদাদের ব্রাহ্মধর্ম পড়াতে। তার গাড়িটিও যেমন ঘোড়াটিও ছিল তেমনি ছোট্ট। আমরা বলাবলি করতুম, ‘ওইটুকু গাড়ির ভিতরে বেচারামবাবু ঢোকেন কেমন করে?’ এ ছিল এক বড় সমস্যা আমাদের কাছে। দূর থেকে গাড়ি আসছে দেখেই চিনতুম—ওই আসছেন বেচারামবাবু, ওই যে তাঁর গাড়ি দেখা যায়। তখন জ্যোতিকা মশায় কোত্থেকে পুরোনো একটা মরচে-ধরা বয়লার কিনেছেন, ‘সরোজিনী’ স্টীমারে বসানো হবে। বয়লারটা পড়ে থাকে গোলচক্করে। একদিন বেচারামবাবু এসেছেন; দাদাদের পড়িয়ে বাড়ি ফিরে যাবেন, ঘোড়া আর খুঁজে পান না। ঘোড়া গেল কোথায়, দেখ দেখ! ঘোড়া হারিয়ে গেছে। বেচারামবাবু হতভম্ব। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল। ঘোড়া বয়লারের ভিতরে ঢুকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। ঘোড়াটা ঘাস খেতে খেতে কখন বয়লারের ভিতরে ঢুকে গেছে আর বের হতে পারছে না। শেষে সহিস লেজ ধরে তাকে বের করে বয়লারটার ভিতর থেকে।
নহবতখানার নিচে ফটকের পাশেই নন্দফরাশের ঘর। ঘরের সামনেই কুয়ো, অনেক কালের পুরোনো, কলের জল হওয়ার আগেকার। কুয়োর পাশে মস্ত শবজিবাগান, খুব নিচু পাঁচিলঘেরা। তার পশ্চিমে ভাগবত মালী আর বেহারাদের ঘর এক সারি। তার উত্তর ধারে গোয়াল, গোয়ালের পুবকোণে মস্ত একটা গাড়িখানা। গাড়িখানার গায়ে পাহাড়ের মতো উচু বিচালির স্তূপ, তার উপরে মেথরদের ছাগলছানাগুলি লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়। আমরাও উঠতে চেষ্টা করি মাঝে মাঝে। সেটি থেকে একটু দূরে বাড়ির ঈশান কোণে বিরাট একটা তেঁতুলগাছ, সে যে কত দিনের কেউ বলতে পারে না। দৈত্যের হাতের মত তার মোটা মোটা কালো ডাল। এ-বাড়িতে ও-বাড়িতে যত ছেলেমেয়ে জন্মেছি তাদের সবার নাড়ি পোঁতা ছিল ওই গাছের তলায়। সেই তেঁতুলগাছের ছায়ায় ছিরু মেথরদের ঘর। তাদের তিন পুরুষ ওখানে বসবাস করছে আমাদের সঙ্গে। তাদের ঘরের পিছনে জোড়াসাঁকোর বাড়ির উত্তর দিকের পাঁচিল; তার গায়ে তিনটে বড় বড় বাদামগাছ, যেন শহরের আর সব বাড়ি আড়াল করে মাথা তুলে উত্তর দুয়ার পাহারা দিচ্ছে। চাকররা সেই বাদামগাছ থেকে আমাদের জন্য পাতবাদাম কুড়িয়ে আনে। উত্তর-পশ্চিম দিকটা কথায় বোঝাতে হলে তিন-চারটে পাড়ার নাম করতে হয়— মালীপাড়া, গোয়ালপাড়া, ডোমপাড়া, এমনি, তবে ঠিক ছবিটা বোঝাতে পারি। আস্তাবলে যেমন ছিল সমশের কোচোয়ান কর্তা, একতলায় নন্দফরাশ, মালীপাড়ায় রাধামালী, গোয়ালপাড়ায় রামগয়লা, তেমনি ডোমপাড়ায় ছিরুমেথরের একাধিপত্য। এই এক-এক পাড়ার এক-এক অধিকারীর কথা বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। দু-একটা বলি শোনো।
নন্দফরাশের দরবারের বর্ণনা তো দিয়েছি। সমশের কোচোয়ানের কথাও তো হল। দরোয়ান-বেহারাদের দোলের কথা, মালীদের চিতাবাড়ি তাও বলেছি। এবারে বলি তবে ছিরুমেথরের চরিত্র। তাদের ঘর খোলা দিয়ে ছাওয়া; বাদামতলায় কাত হয়ে পড়েছে ঝড়ে জলে। সারাদিনমান তেঁতুলগাছের ছায়াতেই ঢাকা সেই কোণটা; রোদ পড়তে দেখিনে। হ্যাংলা কুকুরছানাগুলোর ডাক এসে পৌঁছয় সেদিক থেকে কানে। কুকুরের তাড়া খেয়ে হাঁস মুরগি থেকে থেকে ক্যাঁ-ক্যাঁ চীৎকার ছাড়ে। সেই ছায়ায় অন্ধকারে ছিরুমেথরের ঘরের দাওয়া দেখা যায়। একধারে একটা জলের জালা, আধখানা তার মাটিতে পোঁতা। সেই ঠাণ্ডা জালার জলে কাজের শেষে ছিরুমেথর চান করে দেখি। কালো তার রঙ। ভারি শৌখিন ছিল ছিরুমেথর। কালো হলেও ছিরুর চেহারা ছিল বেশ; কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, মুখের কাটকোটও সুন্দর। বিলিতি মদ খাওয়া তার অভ্যেস ছিল। দেশি মদ ছুঁ’ত না। বিলিতি মদ খেলেই তার মুখে ফর্ ফর্ করে ইংরেজি গরম গরম গালাগালি বের হয়— ড্যাম ইউ রাস্কেল। ইংরেজি বুলি শুনলেই বোঝা যেত লোকটা ‘খেয়েছে’। বাড়ি রাস্তাঘাট পরিপাটি রাখা কাজ ছিল তার। সামনের রাস্তা ঝাঁট দিয়ে চলে গেল যেন ধুলোর উপরে আলপনা এঁকে দিলে ঝাঁটা দিয়ে, জলে ঢেউ খেলিয়ে দিলে। রাস্ত ঝাঁটানোর আর্টিস্ট তাকে বলা যেতে পারে। একদিন হল কি, বাড়িরই কে যেন ডেকেছে ছিরুকে। দরোয়ান গেছে ডাকতে। সে ছিল মউজে; যে মেথরটা হুকুম শুনবে সে তখন তো নেই, ইংরেজি-বুলি-বলা আর একটা মানুষ তার মধ্যে বসে আছে। দরোয়ান যেই না কাছে গিয়ে তাকে ডাক দিয়েছে অমনি ছিরু শুরু করেছে ইংরেজিতে গালাগালি। কিছুতেই আর তাকে থামানো যায় না। তখন দরোয়ানও হিন্দি বুলিতে তেরিমেরি করে যেমন লাঠি তোলা—বাস্, সাহেবের অন্তর্ধান। ছিরুমেথরের মধ্যেকার ভেতো বাঙালিটা হঠাৎ ফিরে এসে দরোয়ানজির পায়ে ধরতে চায়, ‘মাপ করে, দরোয়ানজি, ঘাট হয়েছে।’ ‘আরে ছুঁয়ো মৎ, ছুঁয়ো মৎ’ বলে দরোয়ান যত পিছয় ছিরু তত এগিয়ে আসে। শেষে দরোয়ানের ভঙ্গ দিয়ে পলায়ন জাত যাবার ভয়ে। ছিরুর বুদ্ধি দেখে আমরা অবাক। দরোয়ান মেথরে এ প্রহসন প্রায়ই দেখতুম আর হাসতুম। ছিরুর আর এক কীর্তির কথা ছোটপিসেমশায় বলতেন, ‘জানিস? মল্লিকবাড়িতে বিয়ের মজলিসে গেছি। দেখি, শিমলের ধুতিচাদর জুতোমোজা পরে ফিট্বাবু সেজে ছিরুটা মজলিসের একদিকে বসে সটকা টানছে, আমাকে দেখেই দে চম্পট।’
বাবুয়ানি কায়দার দোরস্ত ছিল ছোট বড় খানসামা চাকর পর্যন্ত সবাই জোড়াসাঁকোর বাড়ির। ভদ্রলোক কেউ বাড়িতে এলে খাতির করে বসাতে জানত। এখন সে-রকম চাকরবাকর দুর্লভ। নতুন চাকররা পুরানো চাকরদের হাতে কি রকম ভাবে কায়দাকানুন তরিবত শিখত দেখো। বাবামশায়ের ছোট বেয়ারা মাদ্রাজী। নতুন এসে সে একদিন লুকিয়ে বাবামশায়ের গেলাসে বরফজল খেয়েছে। বুদ্ধুর নজরে পড়ে গেছে তার সে বেয়াদবিটি। বাবুর গেলাসে বরফজল খাওয়া, বসাও পঞ্চায়েত, দাও দণ্ড। বেচারা কেঁদেই অস্থির, বসল পঞ্চায়েত বেয়ারাদের মহলে। অনেক রাত পর্যন্ত চলল তক্কাতক্কি। একটা ভোজের টাকা দিয়ে, মাথা নেড়া করে, টিকি রেখে তবে উদ্ধার পায় সে। এই রীতিমত দণ্ডের টাকাটা কার কাছ থেকে এসেছিল বলতে পার? বাবামশায়ের কাছেই ছোঁড়াটা নিজের দোষ স্বীকার করে কেঁদে কেটে এই টাকাটা বার করেছিল। চাকরদের বাবুয়ানি শিক্ষার খরচা বাবুদেরই বহন করতে হত।
বুদ্ধুবেয়ারা ভালোমানুষ হলেও বাবুর জিনিসপত্রের বিষয়ে খুব হুঁশিয়ার ছিল। যার রুমালে ল্যাভেণ্ডারের গন্ধ পাবে নিয়ে বাবামশায়ের আলমারিতে তুলে রাখবে। মণিখুড়োর রুমাল নিয়ে একদিন এইরকম তুলে রেখেছে; বলে, ‘এতে বাবুর খোসবো আছে যে।’ মণিখুড়ো বলেন, ‘তা বাবুর কাছ থেকেই চেয়ে নিয়ে খোসবো রুমালে মাখিয়েছিলুম আমি—রুমালটা আমারই। ধোপাবাড়ির নম্বর দেখো।’ বুদ্ধু তখন সেই রুমাল ফিরিয়ে দেয় মণিখুড়োকে। বড় বিশ্বাসী বেয়ারা ছিল, এমন আজকাল আর দেখা যায় না। বাবামশায়ের কোনো জিনিস কখনও এদিক-ওদিক হতে পারত না। কেমন সরল বিশ্বাসী ছিল বুদ্ধু, তা বলছি। একবার বাবামশায় গেছেন ইংরেজি থিয়েটারে; আঙুলে হীরের আংটি—বনস্পতি হীরে, খুব দামী; আর হাতে একটি লাঠি, তার মাথায় কাটগ্লাসের একটি লম্বা এসেন্সের শিশি, শখের লাঠি ছিল সেটি। বাবামশায় ফিরে এসে লাঠি আংটি বুদ্ধুর হাতে দিয়ে শুয়ে পড়েছেন। কয়দিন পর আংটি দপ্তরখানায় পাঠানো হবে, হীরেটি নেই। নেই তো নেই; কতদিন ধরে খোঁজাখুঁজি, কোথায় যে পড়েছে তার পাত্তা পাওয়া গেল না। গরমিকাল এসে গেল। এই সময়ে বাবামশায় যেমন ফি বছর একবার করে আলমারি খালি করেন তেমনি খালি করছেন—বাবামশায় হাতের কাছে জামা কাপড় যা পাচ্ছেন সব টেনে টেনে ফেলছেন, যে যা পাচ্ছে নিয়ে নিচ্ছে। খালি করতে করতে আলমারির বাকি রইল মাত্র কয়েকটি সাদা ধুতি আর পাঞ্জাবি। তার তলা থেকে বের হল সেই হারানো হীরে। বাবামশায় সেটি হাতে নিয়ে বললেন, ‘বুদ্ধু, এই তো সেই হীরে। তুই এখানে রেখে দিয়েছিস, আর এর জন্য কত খোঁজাখুঁজি হচ্ছে। বুদ্ধু বললে, ‘তা আমি কি জানি ওটি হীরে। সকালে ঘরে কুড়িয়ে পেলুম, ভাবলুম ঝাড়ের কাচ। তুলে রেখে দিলুম।’
এইবার শোনো রান্নাবাড়ির গল্প। গলির ভিতরে ছোট্ট ঘর, অমৃতদাসী সেই ঘরে বসে জাঁতায় সোনামুগের ডাল ভাঙে আর বাটনা বাটে। এবারে যখন বাড়ি ভাঙে দেখেই চিনলুম—আরে, এই তো সেই অমৃতদাসীর ঘর। ছেলেবেলায় সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিবিষ্টমনে তার ডাল ভাঙা দেখতুম। সোনার বর্ণ সোনামুগের ডাল জাঁতার চারিদিক দিয়ে সোনার ঝরনার মত ঝরে পড়ত। মাঝে মাঝে অমৃতদাসী একমুঠো ডাল হাতে তুলে দিত, বলত, ‘খাবে খোকা? খাও, এই নাও।’ অল্প অল্প করে সেই ডাল মুখে ফেলে চিবতুম, বেশ লাগত। সেই ঘরটি আর জাঁতাটি, সারাজীবন তাই নিয়েই কেটেছে; তার মিউজিক ছিল জাঁতার ঘড়ঘড়নি। সোনামুগ আর বাটনার হলুদের জল ভেসে যাচ্ছে, কাপড়েও লেগেছে, সোনাতে হলুদে মাখামাখি। এখনও মনে হয় তার কথা; দুঃখিনী একটি বুড়ির ছবি চোখে ভাসে।
বাসনমাজানি এল দুপুরে, বাসন মেজে রেখে গেল যার যার দোরে, সোনার মত ঝকঝক করছে। দুধ জ্বাল দেবার দাসী দুধ জ্বাল দিচ্ছে; দুধের ফেনা তুলছে তো তুলছেই। জাল দিয়ে বাটিতে বাটিতে দুধ ভাগ করে রাখছে। তার পর দিব্যঠাকুর হাতা বেড়ি দিয়ে রান্নায় ব্যস্ত। ওদিকটায় আর যেতুম না বড়।
রান্নাবাড়ির ঠিক উপরে ঠাকুরঘর। সেখানে ছোটপিসিমা ব’সে, মহিম কথক কথকতা করছেন, সিংহাসনে ঠাকুর অলকাতিলকা পরে মাথায় রুপোর মুকুট দিয়ে। এখনও সে-সবই আছে, কেবল ছোটপিসিমা নেই, মহিম কথক নেই। সেখানে হত পুরাণের গল্প। সেখান থেকে নেমে এসে ছোটপিসিমার ঘরে ছবি দেখতুম। একটু আগে যা শুনে আসতুম উপরে, নিচে তারই ছবি সব চোখে দেখতুম। সেই পুরাণের পুঁথি কিছু এখনও আছে আমার কাছে, ছেলেরা সেদিন কোন্ কোণা থেকে বের করলে। দেখেই চিনলুম, এ যে মহিম কথকের পুঁথি, এক-একটি পাতা পড়ে যেতেন কথকঠাকুর আর এক-একটি ছবি যেন চোখের সামনে ভেসে উঠত। লাল বনাত একখানা গায়ে দিয়ে বসতেন পুঁথি পড়তে, হাতে রুপোর আংটি, হাত নেড়ে নেড়ে কথকতা করতেন। রুপোর আংটির ঝক্ঝকানি এখনও দেখতে পাই। আঁকতে শিখে সে ছবি একখানা এঁকেওছিলুম।
বাবামশায়ের সকালের মজলিস বসত দোতলায় দক্ষিণের বারান্দায়। দক্ষিণের বাগানে ভাগবত মালী কাজ করে বেড়াত। বাবামশায়ের শখের বাগানের মালী, নিজের হাতে তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি করেছিলেন। যেখানে যত দুর্মূল্য গাছ পাওয়া যায় বাবামশায় তা এনে বাগানে লাগাতেন, বাগান সম্বন্ধে নানারকমের বই পড়ে বাগান করা শিখেছিলেন, ওই ছিল তার প্রধান শখ। কি সুন্দর সাজানো বাগান, গাছের প্রতিটি পাতা যেন ঝকঝক করত। হর্টিকালচারের এক সাহেব বললেন, ‘এদেশে টিউলিপ ফুল ফোটে না, তার অনেক চেষ্টা করে দেখেছেন।’ বাবামশায় বললেন, ‘আচ্ছা, আমি ফোটাব।’ বিলেত থেকে সেই ফুলের গেঁড় আনলেন, নানারকমের সার দিলেন গাছের গোড়ায়; কাচের না কিসের ঢাকা দিলেন উপরে। বাবামশায়ের উদ্ভিদবিদ্যা সম্বন্ধে বড় বড় বই এখনও নিচের তলায় আলমারি ঠাসা। কত বই দেশ বিদেশ থেকে আনিয়ে পড়েছেন। গাছ সম্বন্ধে যে বইটি তিনি সর্বদা পড়তেন, সোনার জলে বাঁধানো, সবুজ চামড়ায় মোড়া, যেন কত মূল্যবান একটি কবিতার বই। বড় হয়ে খুলে দেখি সেটি হারপার কোম্পানির নানারকম ফল ফুল গাছের সচিত্র তালিকা। তা টিউলিপের গেঁড় লাগানো হল, ভাগবত মালীকে শিখিয়ে দিলেন, রোজ তাতে কি করবে, কি করে যত্ন নিতে হবে। তিনিও নিজেও এসে একবার দুবার করে দেখে যান। একদিন সেই ফুল ফুটল—একটি ফুল। ফুল ফুটেছে, ফুল ফুটেছে! ওই একটি ফুলের জন্য বাড়িতে হৈ-চৈ পড়ে গেল। সবাই আসে দেখতে। যে ফুল ফোটে না এই দেশে সেই ফুল ফুটল শেষে। বাবামশায় খুব খুশি । ফুল ফোটাতে শখ হয়েছিল, ফুল ফুটল। হর্টিকালচারের সাহেব খবর শুনে ছুটে এলেন। তিনি অবাক। কত চেষ্টা করেও তাঁরা পারেননি। বললেন, ‘একজিবিশনে দেখাতে হবে।’ শিগগিরই হর্টিকালচারের একজিবিশন হবে। ভাগবত রঙিন চাদর বেঁধে পরিষ্কার ধুতিজামা পরে তৈরি হয়ে এল, তাকে দিয়ে ফুল পাঠানো হল। একজিবিশনে সেই ফুলটির জন্য একটি সোনার মেডেল পেলেন বাবামশায়। সেই সোনার মেডেল আর একটি গাছকাটা কাঁচি ভাগবতকে তিনি বকশিস দিলেন। বললেন, ‘নে মেডেলটা তুইই গলায় ঝোলা।’ মেডেলটা দিয়ে এক সময়ে হয়তো সে ছেলের গয়না গড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু কাঁচিটি কখনও ছাড়েনি। আমাদের কতবার বলত, ‘বাবুর দেওয়া এই কাঁচি।’
সেদিন বড় মজা লাগল। এই কিছুদিন আগের কথা। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বারান্দায় বসে আছি। ভাগবত মরে গেছে অনেকদিন আগে, তার ছেলে এখন বাগানে কাজ করে। বাগানের কোণায় ছিল করবীগাছ। ছোট ছেলে বাপের হাতের সেই কাঁচি নিয়ে তার ডাল ছাঁটবার চেষ্টা করছে, কিছুতেই আর সামলাতে পারছে না, হাত আগডালে পৌঁছয় না তার। গাছের ডালপাতা হাওয়াতে দুলে দুলে ছেলেটিকে জাপটে ধরছে, কাঁচি হাতে সে তার ভিতরে আটকা প’ড়ে অস্থির। বসে আমি মজা দেখছি আর হাসছি। মোহনলাল শোভনলাল যাচ্ছিল সেখান দিয়ে, তাদের বললুম, ‘ওরে দেখ, মজা দেখ, ভাগবতের ছেলে তার বাপের লাগানো গাছের সঙ্গে কেমন খেলা করছে দেখ। যেন দুষ্টু ছেলের চুল কাটবে নাপিত, ছেলে মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে হেলিয়ে দুলিয়ে নাপিতকে নাস্তানাবুদ করে দিচ্ছে। বলে দে ওকে, গাছের ডাল কাটবার দরকার নেই। ও-গাছ অমনি থাকুক।’ বাপের গাছের সঙ্গে ছেলে খেলা করছে দেখে ভারি ভালো লেগেছিল।
ছেলেবেলায় বাবামশায়ের শখের বাগানে কেউ আমরা ঢুকতে পেতুম না, ভাগবত মালীর দাপটে। আমরা ছেলেরা কয়জনে মিলে একপাশে নিজেদের বাগান বানিয়ে নিয়েছিলুম। ছোট্ট বাগানটি, বাবামশায়ের দেখাদেখি একটা জায়গায় ইঁট পাথর জড়ো করে এখানে ওখানে ঘাসের চাপড়া বসিয়ে পাহাড়ের অনুকরণ করে, মাঝে মাটি খুড়ে একটা গোল মাটির গামলা বসিয়ে তাতে জল ভরে টিনের হাঁস মাছ ছেড়ে চুম্বক কাঠি দিয়ে টানি—সেই হল আমাদের গোলপুকুর। বিকেলে ইস্কুল থেকে সব ছেলে ফিরে এলে তখন আবার সবাই একসঙ্গে হয়ে খেলাধুলো করি। সারাদিন একলা থাকার পর ওই সময়টুকু বড় আনন্দে কাটত আমার।
বিকেল হতেই বাগানে বাবামশায়ের কুরসি ফরসি পড়ে। ভাগবত ফোয়ারা ছেড়ে দেয়; সত্যিকার হাঁস মাছ ফেয়ারার জলে ভেসে বেড়ায়। বাবামশায় নিচে নেমে এসে বসেন বাগানে। পড়শি কালাচাঁদবাবু, মাথায় বুলবুলির ঝুঁটির মত একটু চুল, বুকে একটি ফুল গুঁজে, গলায় চুনটকরা চাদর ঝুলিয়ে, বার্নিশকরা জুতো প’রে, ছিপছিপে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে হেলেদুলে আসেন বাগানের মজলিসে। ফি শনিবার আপিস ছুটির পর মতিলালবাবু চলে আসেন বাবামশায়ের কাছে। মাছ ধরার খুব ঝোঁক ছিল তাঁর। বাবামশায় বলতেন, ‘এই যে লালমোতি এসেছ, ছিপটিপ ঠিক আছে তো?’ লালমোতি বলেই ডাকতেন তাঁকে। ওদিককার বড় পুকুরে লালমোতি প্রায়ই মাছ ধরতেন। বাবামশায়ও বসে যেতেন মাছ ধরতে কোনো-কোনোদিন। ওই সেই পুরানো পুকুর যার ওপারে প্রকাণ্ড বটগাছ— রবিকার ‘জীবন-স্মৃতিতে’ আছে লেখা। ছেলেবেলায় যা ভয় পেতুম বটগাছটাকে। গল্প শুনতুম চাকরদাসীর কাছে, জটেবুড়ি ব্রহ্মদত্তি কত কি আছে ওখানে।
তা যাক, তখন সেই বিকেলবেলা ওদিকে বাগানে জমত বাবামশায়ের আসর, এদিকে আমাদের হত ইস্কুল-ইস্কুল খেলা। এ-বাড়ি ও-বাড়ির মাঝে যে গলিটুকু কাছারিঘরের সামনে, সেই জায়গাটুকুই আমাদের খেলার জায়গা। কোত্থেকে একটা ভাঙা বেঞ্চি জোগাড় করে তাতে সবকটি ছেলে ঠেসাঠেসি করে বসি, দীপুদা মাস্টার। গলির মোড়ে সেই সময়ে হাঁক দিতে দিতে ভিতরে আসে চিনেবাদাম, গুলাবি রেউড়ি, ঘুগনিদানা, লজেঞ্জুস, কত কি— ‘খায় দায় পাখিটি বনের দিকে আঁখিটি’, বেঞ্চিতে বসে বসে সেই দিকেই নজর আমাদের। কতক্ষণে গুলাবি রেউড়ি চিনেবাদামওয়ালা আসে। দেউড়ির কাছে যেমন তারা এসে দাঁড়ায়, দে ছুট ইস্কুল-ইস্কুল খেলা ছেড়ে। দীপুদা ভাঙা কাঠের চেয়ারে বসে গভীর সুরে বলেন, ‘পড়্ সবাই।’ পড়া আর কি, কোলের উপর ঠোঙা রেখে তা থেকে চিনেবাদাম বের করে ভাঙছি আর খাচ্ছি; দীপুদার হাতেও এক ঠোঙা, তিনিও খাচ্ছেন। এই হত আমাদের পড়া-পড়া খেলা। একদিন আবার প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন হল। কে প্রাইজ দেবে। উপরে বারান্দায় পায়চারি করছেন রবিকা। তিনি আসতেন না বড় আমাদের খেলায় যোগ দিতে। সমান বয়সের ছেলেও তো থাকত এই খেলায়। কিন্তু তিনি ওই তখন থেকেই কেমন একলা একলা থাকতেন, একলা পায়চারি করতেন। সেখান থেকেই মাঝে মাঝে দেখতেন দাঁড়িয়ে, নিচে আমরা খেলা করছি। গিয়ে ধরলুম তাকে, ‘আমাদের ইস্কুলে প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন হবে, তোমায় আসতে হবে।’ রবিকা একটু হেসে নেমে এলেন, প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশন হল। চিনেবাদাম গুলাবি রেউড়ির ঠোঙা। প্রাইজের পরে আবার তিনি দাঁড়িয়ে বক্তৃতাও দিলেন একটি খুব শুদ্ধভাষায়। আহা, কথাগুলো মনে নেই, নয়তো বড় মজাই পেতে তোমরা।
কালে কালে সেই জোড়াসাঁকোর বাড়ির কত বদলই না হল। আমাদের কালেই সেই তোশাখানা হয়ে গেল ড্রামাটিক ক্লাবের নাট্যশালা। ভিস্তিখানায় টেবিল পড়ত, খাওয়াদাওয়া হত। দপ্তরখানা হল গ্রীনরূম। দেউড়ি তো উঠেই গেল, ভেঙেচুরে লম্বা ঘর উঠল। খামখেয়ালির বৈঠক বসত সেখানে। একবার ‘বৈকুণ্ঠের খাতা’ অভিনয় হল, বাড়ির ছেলেদের দিয়ে করিয়েছিলুম, গাড়িবারান্দায় মনোহর সিঙের দোল-উৎসব হত যেখানে, সেইখানে মস্ত স্টেজ তৈরি হল— ঘোড়াসুদ্ধ গাড়ি সোজা এসে ঢুকল স্টেজে। টং টং করে আপিসফেরত অবিনাশবাবু নামলেন এসে। ব্যাপার দেখে অডিয়েন্স একেবারে অবাক।
কত অভিনয় কত খেলা ক’রে, কত সুখদুঃখের দিন কাটিয়ে, সেই জোড়াসাঁকোর বাড়ি মাড়োয়ারি ধনীকে বেচে বের হতে হল যেদিন আমার নিজের ছেলেপিলে বউঝি নিয়ে, সেদিন সেই তেঁতুলতলায় মেথরের নাতি নাতনি নাতবউ কেবল তারাই এসে আমায় ঘিরে কান্না জুড়লে। তাদের ওইখানেই জন্ম, ওইখানেই মৃত্যু। দেশ ঘর বলে আর কিছু নেই। বলে, ‘এখন উপায় কি হবে বাবু? আমাদের তুলে দিলে কোথায় যাব?’ আমি বলি, ‘চল্ আমার সঙ্গে বরানগরে, সেইখানে তোদের ঘর বেঁধে দেব। তোরা থাকবি, কাজ করবি, যেমন করছিলি এইখানে।’ সেই পুরোনোকালের তেঁতুলতলার মায়া ছাড়তে পারলে না। আজও সেখানে তারা রয়ে গেছে কিনা কে জানে।
কি সুখের স্থানই ছিল, কি সুখের হাওয়াই বইত ওইটুকখানি জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। ওখানের মায়ায় যে শুধু আমিই পড়েছিলেম তা নয়, চাকরদাসী কর্মচারী ছেলেবুড়ো সবাই। এই একটি কথা বলি, এ থেকেই বুঝে নাও। মনোরঞ্জনবাবু যশোরের কুটুম্ব; কাছারিতে কাজ করেন, বাতে একটি পা পঙ্গু। তেঁতুলতলায় কর্মচারীদের বাসস্থান, তারই একটি ছোট্ট ঘরে তিনি থাকেন। পেনশন হবে হবে, পড়ল বুড়ো নির্ঘাত রোগে। খবর পেয়ে ছুটি দেখতে বুড়োকে—ছোট্ট ঘর, একটি মাত্র দরজা জাল দেওয়া, দেয়ালে আর কোনো পথ নেই যে হাওয়া রোদ আসে। বুঝলুম বুড়োর দিন ফুরোবে সেইখানেই।
‘কেমন আছ? একখানা ভালো ঘরে যেখানে হাওয়া রোদ পাও সেই ঘরে যাও।’
‘আজ্ঞে, বেশ আছি এখানে। দু-এক দিনের মধ্যেই সেরে উঠে কাছারিতে যাব।’
বলি, ‘বাসাবাড়িটা একবার তদারক করে যাই।’ ঘুরতে ঘুরতে দেখি পায়রার খোপের মত একটিমাত্র ভাঙা দেয়ালের গায়ে জালবদ্ধ দরজার ধারে মনোরঞ্জনবাবু গোটা গোটা অক্ষরে খড়ি দিয়ে লিখে রেখেছেন ‘মনোরঞ্জন কারাগার’। ঘরে এলেম। তার পরদিন শুনি মনোরঞ্জনবাবুর মনোরঞ্জন-কারাগারবাস শেষ হয়ে গেছে। কি বস্তু জোড়াসাঁকোর বাড়ি বুঝে দেখো। কারাগার হলেও সে মনোরঞ্জন। জোড়াসাঁকোর পারে ধরা ‘মনোরঞ্জন কারাগার’।
০৬. পলতার বাগান
পলতার বাগান মনে প’ড়ে দুঃখও পাচ্ছি আনন্দও পাচ্ছি। কতই বা বয়েস তখন আমার। বেশ চলছিল, হঠাৎ একদিন সব বন্ধ হয়ে গেল, ঘরে ঘরে তালা পড়ল। বড়পিসেমশায় ছোটপিসেমশায় আমাদের সবাইকে নিয়ে বোটে রওনা হলেন। দারুণ ঝড়, নৌকো এ-পাশ ও-পাশ টলে, ডোবে বুঝি বা এইবারে। বড়পিসিমা ছোটপিসিমা আমাদের বুকে আঁকড়ে নিয়ে ডাকতে লাগলেন, ‘হে হরি, হে হরি!’ এলুম আবার জোড়াসাঁকোর বাড়িতে। দোতলার নাচঘরে ছিল জ্যেঠামশায়ের বড় একখানি অয়েলপেন্টিং, বসে আছেন সামনের দিকে চেয়ে। ছোটপিসিমা বড়পিসিমা আছড়ে পড়লেন সেই ছবির সামনে, ‘দাদা, এ কী হয়ে গেল আমাদের!’
অদ্ভুত কাণ্ড। যেন চলতে চলতে হঠাৎ সামনে একটা দেয়াল পড়ে গেল; সব কিছু থেমে গেল, ঘড়িটা পর্যন্ত। বড় হয়ে যখন গেলুম পলতার বাগানে, দেখি, বাবার সেই শোবার ঘর ঠিক তেমনি সাজানো আছে, একটু নড়চড় নেই—দেয়ালে ঘড়িটি ঠিক কাঁটায় কাঁটায় স্থির, বাবামশায়ের মৃত্যুর সময়টি তখনও ধরে রেখেছে। ঘরজোড়া মেঝেতে সাদা গালচে, তার নকশাটা যেন পাথরের চাতালে ফুলপাতা হওয়ায় খসে পড়েছে। দেয়ালে বেলোয়ারি কাচে রঙিন সব ফুলের মালা, বাতিনেবা গোলাপি রঙের ফটিকের ঝাড়, দেয়ালগিরি, পর্দা, সবই যেন তখনও একটা মহা আনন্দ-উৎসব হঠাৎ শেষ হয়ে যাওয়ার ম্লান বিশৃঙ্খল রূপ ধরে রয়েছে। মা সেখানকার কোনো জিনিস আনতে দেননি। কিন্তু সেই ঘড়িটি সেবারে আমি নিয়ে আসি, এখনও আছে বেলঘরিয়ার বাড়িতে। আশ্চর্য ঘড়ি—কেমন আপনি বন্ধ হয়ে যায়। সেদিনও বন্ধ হয়ে গেল অলকের মা যেদিন চলে গেলেন, ঠিক জায়গায় কাঁটার দাগ টেনে। অলকরা চাবি ঘোরায় ঘড়ি চলে না। অলককে বললুম, ‘ও ঘড়ি তোরা ছুঁসনে, তোদের হাতে বিগড়ে যাবে। আমার সঙ্গে ওর অনেক কালের ভাব। আমি জানি ওর হাড়হদ্দ; আমার কাছে দে দেখি নামিয়ে।’ ঘড়িটি নামিয়ে এনে দিলে কাছে। আমি তাতে হাত দেবা মাত্র ঘড়ি নতুন করে আবার চলতে লাগল। বহুকালের জিনিস, অনেক মৃত্যুর সময় রেখেছে এ-ঘড়ি। মাসির গল্পে পড়নি এ-ঘড়ির কথা? দিয়েছি গল্পে ঢুকিয়ে। এখন আমার হয়েছে ওই—গল্পের মধ্যে ধরে রাখছি আমার আগের জীবন আর আজকের জীবনেরও কথা।
একটি ভাই ছিল আমার—সকলের ছোট, দেখতে রোগা টিংটিঙে, বড় মায়াবী মুখখানি। আমরা ছিলুম তার কাছে পালোয়ান। একটু হুমকি দিলেই ভয়ে কেঁদে ফেলত। বাবামশায় খুব ভালবাসতেন তাকে, আদর করে ডাকতেন ‘র্যাট’। তার জন্য আসত আলাদা চকোলেট লজেঞ্জুস বাবামশায় নিজের হাতে তাকে খাওয়াতেন। মা এক-এক সময়ে বলতেন, এত লজেঞ্জুস খাইয়েই এর রোগ সারে না। বাবামশায়ের ‘র্যাট’ ছিল তার গোলাপি হরিণেরই সামিল, এত আদরযত্ন। হরিণেরই মত সুন্দর চোখ দুটাে ছিল তার।
এখন, সেই ভাই মারা যেতে বাবামশায়ের মন গেল ভেঙে। বললেন, ‘এই জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আর থাকব না। পলতায় তখন সবে বাগান কিনেছেন, সবাইকে নিয়ে জোড়াসাঁকোর বাড়ি ছেড়ে উঠলেন গিয়ে সেখানে। চারিদিকে ঝোপঝাড়, মাঝে বিরাট একটা ভাঙা বাড়ি—এ-দেয়াল সে-দেয়াল বেয়ে জল প’ড়ে ছ্যাতলা ধরে গেছে। বড়পিসিমা বললেন, ‘ও গুনু, এ কোথায় নিয়ে এলি? এখানে থাকব কি করে?’ বাবামশায় বললেন, ‘এই দেখোনা দিদি, কদিনেই সব করে ঠিক ফেলছি।’ মাঝে ছিল দুখানি বড় হল, পাশে ছোটবড় নানা আকারের ঘর, ওরই মধ্যে যে কয়টি বাসযোগ্য ঘর পেলেন তাতেই পিসিমারা সব গুছিয়ে নিয়ে বসলেন। এদিকে লোক লেগে গেল চারদিক মেরামত করতে। বাবামশায়ের ইঞ্জিনিয়ার ছিল অক্ষয় সাহা। বাবামশায় নিজের হাতে প্ল্যান করে করে অক্ষয় সাহার হাতে দেন, তিনি আবার প্ল্যান দেখে দেখে তা তৈরি করান। সেই খাতাটি আমি রেখে দিয়েছি, পলতার বাগানের প্ল্যান তাতে ধরা আছে।
দেখতে দেখতে সমস্ত বাগানের চেহারা গেল ফিরে ফোয়ারা বসল, ফটক তৈরি হল, লাল রাস্তা এঁকেবেঁকে ছড়িয়ে পড়ল। বন হয়ে উঠল উপবন। পুরনো যে বাড়িটা ছিল সেটা হল বৈঠকখানা। সেখান থেকে হাত পঞ্চাশেক দূরে অন্দরমহল উঠল। বৈঠকখানা থেকে বেরিয়েই একটি তারের গাছঘর—নানারকম গাছ, অরকিড ফুল, তারই মাঝে নানাজাতের পাখি ঝুলছে। সেখান থেকে লাল রাস্তাটি, খানিকটা এগিয়ে ফোয়ারা বসানো হয়েছে মাঝখানে, তা ঘিরে চলে গেছে একেবারে অন্দরমহলে। বাবামশায় বিকেল হলে মাঝে মাঝে এসে বসেন ফোয়ারার ধারে। ফেয়ারাটির মাঝে একটি কচি ছেলের ধাতুমূর্তি আকাশের দিকে হাত তুলে, উঁচু হয়ে ফোয়ারা থেকে জল পড়ছে, আশেপাশে পাখিরা গাইছে, ফুলের সুবাস ভেসে আসছে; তারই মাঝে বাবামশায় বসে। মস্ত বড় একটা বিল তৈরি হল একপাশে। যখন কাটা হত দেখতুম মাঝে মাঝে মাটির স্তম্ভ দাঁড়িয়ে আছে পর পর। শ’য়ে শ’য়ে লোক মাটি কাটছে, ঝুড়িতে করে এনে ফেলছে পাড়ে। সেই ঝিল একদিন ভরে উঠল তলা থেকে ওঠা নতুন জলের লহরে। দলে দলে হাঁস চরে বেড়ায়। ঝিলের এক পারে প্রকাণ্ড একটি বটগাছ, তলায় সারস সারসী, ময়ূর ময়ূরী, রুপোলি সোনালি মরাল দলে দলে খেলা করে। তার ওদিকে হরিণবাগান; পালে পালে হরিণ একদিক থেকে আর একদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। তার ও-দিকে মাঠভরা ভেড়ার পাল; তার পর গেল গোরু, মোষ, ঘোড়া, তার পর হল শাকসবজি তরিতরকারি নানা ফসলের খেত। এই গেল একদিকের কথা। আর একদিকে ফুলের বাগান, বাগানে সুন্দর সুন্দর খাঁচা। সে কি খাঁচা যেন এক-একটি মন্দির; সোনালি রঙ, তাতে নানা জাতের রঙবেরঙের পাখি, দেশবিদেশ থেকে আনানো, বাবামশায়ের বড় শখের। বাগানের পরে খেলার মাঠ। তার পর আম কাঁঠাল লিচু পেয়ারার বন; তার পর আরো কত কি, মনেও নেই সব। বাগান তো নয়, একটা তল্লাট। ফ্রেঞ্চ টেরিটরি থেকে আরম্ভ করে বদ্দিবাটির মিলের ঘাট অবধি ছিল সেই বাগানের দৌড়।
সেই তল্লাট দু-মাসের মধ্যেই বাবামশায় সাজিয়ে ফেললেন। অনেক মূর্তির ফরমাশ হল বিলেতে। একটা ব্রোঞ্জের ফোয়ারার অর্ডার দিলেন, পছন্দমত নিজের হাতে এঁকে। পুকুরপাড়ে বোধ হয় বসাবার ইচ্ছে ছিল। ফোয়ারাটি যেন একগোছা ঘাস; তেমনি রঙ, দূর থেকে দেখলে সত্যিকারের ঘাস বলেই ভ্রম হয়। তখনকার দিনে ইণ্ডিয়ান আর্ট বলে তো কিছু ছিল না, বিলিতি আর্টেরই আদর হত সবখানে। পরে আমরা দেখি টি. টমসনের দোকানে বিলেত থেকে তৈরি হয়ে এসেছে সেই ফোয়ারা আর দুটি মানুষপ্রমাণ ক্রীতদাসীর ধাতুমূর্তি বাবামশায়ের ফরমাশি জিনিস। ইন্টারন্যাশন্যাল একজিবিশন হয়, সেখানে তা সাজানো হল। প্রত্যেকটি ঘাসের মুখ দিয়ে ফোয়ারা ছুটছে তালগাছ সমান উঁচু হয়ে। ছ হাজার টাকা শুধু সেই ফোয়ারাটির দাম। সেই একজিবিশন থেকে ফোয়ারাটি মূর্তিটি কোন দেশের এক রাজা কিনে নিলেন। ভালো ভালো ফুলদানি, কাচের ফুলের তোড়া, দেখলে তাক লাগে। জ্যেঠামশায় এলেন পলতার বাগানে; বাবামশায় ঘুরে ঘুরে তাকে সব দেখাতে লাগলেন। দেখতে দেখতে বাবামশায়ের ঘরে এলেন। সেই ঘরে ঢুকে জ্যেঠামশায় বললেন, ‘বাঃ গুনু, তোমার মালী তো চমৎকার তোড়া বেঁধেছে। যাবার সময়ে আমাকে এমনি একটি তোড়া বেঁধে দিতে বোলো।’ বাবামশায় বললেন, ‘এ কাচের ফুল, বড়দা তুমি বুঝতে পারনি?’ জ্যেঠামশায়ের তখন হো-হো করে হাসি, ‘আমি আচ্ছা ঠকেছি তো। একটুও বুঝতে পারিনি।’
বাবামশায় প্রায়ই কলকাতায় যেতেন, নানারকম জিনিসপত্তর কিনে নিয়ে আসতেন। একদিন এলেন, একঝাঁক হাঁস নিয়ে, ঠিক যেন চিনেমাটির খেলনার হাঁস; মুঠোর মধ্যে তা পোরা যায়, সাদা ধবধব করছে। সেই হাঁসগুলি নিয়ে নিয়ে ছেড়ে দেওয়ালেন ঝিলে; খেলা করতে থাকবে, সেইখানেই বাসা বাঁধবে, বাচ্চ পাড়বে জলের কিনারায় ঘাসের ঝোপে। পরদিন ভোরে গেছেন হাঁসগুলিকে খাওয়াতে ; দেখেন একটি হাঁসও বেঁচে নেই, ঝিলের জলে রাশ রাশ সাদা সাদা পালক ছেঁড়া পদ্মের পাপড়ির মত ভাসছে। ছোটপিসিমা বললেন, ‘তোর যেমন কাণ্ড, অতটুকু-টুকু হাঁসগুলোকে এমনি ছেড়ে রাখে? রাতারাতি শেয়ালে সব খেয়ে গেছে।’
আর একবার মনে আছে, বাবামশায় বসে আছেন ফোয়ারার ধারে। অন্দরমহলের সামনে বড় বড় প্যাকিং বাক্স এসেছে, চাকররা খুলছে হাতুড়ি বাটালি দিয়ে। প্রায়ই নানা জায়গা থেকে এইরকম প্যাকিং বাক্স আসে বাবামশায়ের ফরমাশি জিনিসে ভরা। তিনি কাছে বসে চাকরদের দিয়ে তা খোলান; আমার খুব ভালো লাগে দেখতে কী বের হয় বাক্সগুলো থেকে। চাকরদাসীদের এড়িয়ে কখনও কখনও সেখানে গিয়ে দাঁড়াই। তা সেদিন বের হল বাক্স থেকে দুটি কাচের ফুলদানি, একটি গোলাপি ডাটার উপর টিউলিপফুল, ফুলে শিশির পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা, দুপাশে দুটি সোনালি পাতা উঠে দু দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। মার চুল বাঁধবার গোল একটি আয়না ছিল, পরে মা সেটি অলকের মাকে দিয়ে দেন। তিনি যতদিন ছিলেন তাতেই মুখ দেখেছেন। এখন সেই আয়নার যা দুর্দশা; আমার ঘরে এনে রেখে দিয়েছে, তার সামনে চুল আঁচড়াতে যাই, কেমন করে ওঠে মন। বলি, ‘আর কেন, নিয়ে যা একে এ ঘর থেকে।’ সেই আয়নার সামনে থাকত টিউলিপফুলের ফুলদানিটি, বরাবর দেখেছি তা। মাঝে একবার এক চাকর সেটি বাজারে নিয়ে গেছে বিক্রি করতে। আর-একটি চাকর খোঁজ পেয়ে তাড়াতাড়ি উদ্ধার করে আনে। আমি বললুম ‘ও পারুল, এটা যত্নে তুলে রাখে। এ কি জিনিস, তা তোমরা বুঝবে না, মা চুল বাঁধতে বসতেন, টিউলিপফুলের ছায়া আর মার মুখের ছায়া এই দুটি ছায়া পড়ত আয়নাতে। এখনও যেন দেখতে পাই সেই ছবি। সোনালি পাতা দুটি এখনও তেমনি ঝকঝক করছে। আমার বাল্যস্মৃতিতে এই টিউলিপফুল ও আয়নার কাহিনী আরো স্পষ্ট লেখা আছে। আর অন্য ফুলদানিটি ছিল, ক্র্যাক্ড চায়না, সবুজ রং, তার গায়ে হাতে আঁকা নীল হলুদ দুটি পাখি আর লতাপাতা কয়েকটি। ভারি সুন্দর সেই ফুলদানিটি থাকত বাবামশায়ের আয়নার টেবিলে। সেটি গেল শেষটায় বউবাজারে, কি হল কে জানে!
বাবামশায় তো এমনি করে বাগানবাড়ি ঘর সাজাচ্ছেন। আমরা ছোট, কিছু তেমন জানিনে বুঝিনে। থাকতুম অন্দরমহলে। মাঝে মাঝে ঈশ্বরবাবু বেড়াতে নিয়ে যেতেন গঙ্গার ধারে বিকেলের দিকে। রাস্তাঘাট তখন ছিল না তেমন। এখানে ওখানে মড়ার মাথার খুলি। চলতে চলতে থমকে দাড়াই। ঈশ্বরবাবু বলেন, ‘ছুঁয়ো-টুয়োনা, ভাই, ও-সব।’ আমরা একটা ডাল বা কঞ্চি নিয়ে খুলিগুলি ঠেলতে ঠেলতে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে বলি, ‘যা, উদ্ধার পেয়ে গেলি।’ ওই ছিল এক খেলা। দু-বেলা হেঁটেই বেড়াতুম।
সেই সময়ে পলতার বাগানে একবার ঠিক হয়, দাদা বিলেতে যাবেন। সাজপোশাক সব তৈরি করবার ফরমাশ গেল কলকাতায় সাহেব দরজির দোকানে। বাবামশায় বললেন, ‘মেজদা আছেন বিলেতে, গগন বিলেত যাক। সতীশ আছে জর্মনিতে, সমর সেখানে যাবে।’ আমাকে দেখিয়ে, বড়পিসিমাকে বললেন, ‘ও থাকুক এখানেই। আমার সঙ্গে ঘুরবে, ইণ্ডিয়া দেখবে, জানবে।’ তখন থেকেই সকলে আমার বিদ্যেবুদ্ধির আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। বুঝেছিলেন, ওসব আমার হবে না। বিদেশ তো যাওয়াই হল না, এদেশেও আর বাবামশায়ের সঙ্গে ঘোরা হয়নি। তবে বাবামশায় যে বলেছিলেন ‘ইণ্ডিয়া দেখবে জানবে’, তা হয়েছে। ভারতবর্ষের যা দেখেছি চিনেছি তিনি থাকলে খুশি হতেন দেখে।
পলতার বাগানে মাস ছয়েক কেটেছে; বাগান সাজানো হয়েছে। বিনয়িনীর বিয়ের ঠিকঠাক, এবারে জামাইষষ্ঠীর দিন পাত্র দেখা হবে। বাবামশায়ের ইচ্ছে হল বন্ধুবান্ধব সবাইকে বাগানে ডেকে পার্টি দেবেন। আয়োজন শুরু হল, যেখানে যত আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সাহেবসুবো, কেউই বাদ রইল না। কেবল আসতে পারেননি একজন, বলাই সিংহ, বাবামশায়ের ক্লাসফ্রেণ্ড। শেষ বয়েস অবধি তিনি যখনই আসতেন, দুঃখ করতেন, বলতেন, ‘কেন গেলুম না আমি। শেষ দেখা দেখলুম না।’ যাক সে কথা। এখন বিরাট আয়োজন হল। এত লোক আসবে দু-তিন দিন থাকবে বুঝতেই পার ব্যাপার। দিকে দিকে তাঁবু পড়ল। কেক-মিষ্টান্নে, ফুলে-ফলে, আতর-গোলাপে ভরে গেল চারদিক। নাচগানেরও ব্যবস্থা হয়েছে। আমরা ঘোরাঘুরি করছি অন্দর-মহলে। বাবুর্চি-খানসামা টেবিল ভরে স্যাণ্ডউইচ আইসক্রিম সাজাচ্ছে। ছেলেমানুষ খাবার দেখে লোভ সামলাতে পারিনে। ঘুরে ফিরেই সেখানে যাই। নবীন বাবুর্চি এটা সেটা হাতে তুলে দেয়, বলে, ‘যাও যাও, এখান থেকে সরে পড়।’ চলে আসি, আবার যাই। এমনি করে আমাদের সময় কাটছে। ওদিকে বৈঠকখানায় শুরু হয়েছে পার্টি, নাচ, গান। রবিকা, জ্যেঠামশায় ওঁরাও ছিলেন; রবিকার গান হয়েছিল। প্রথম দিন দেশি রকমের পার্টি হয়ে গেল। দ্বিতীয় দিন হল সাহেবসুবোদের নিয়ে ডিনার পার্টি। আমাদের নীলমাধব ডাক্তারের ছেলে বিলেতফেরত ব্যারিস্টার নন্দ হালদার সাহেব টোস্ট প্রস্তাবের পর গ্লাস শেষ করে বিলিতি কায়দামাফিক পিছন দিকে গ্লাস ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। অমনি সকলেই আরম্ভ করে দিলেন গ্লাস ছুঁড়ে ফেলতে। একবার করে গ্লাস শেষ হয় আর তা পিছনে ছুঁড়ে ফেলছেন ঝন্ন্ন্ শব্দে চারদিক মুখরিত করে। মনে আছে, খানসামারা যখন লাইন করে করে সাজাচ্ছিল কাচের গ্লাস—গোলাপি আভা, খুব দামি। পরদিন সকালে যখন ঝাটপাট শুরু হল গোলাপের পাপড়ির সঙ্গে গোলাপি কাচের টুকরো স্তূপাকার হয়ে বাইরে চলে গেল। দু-তিনদিন পরে পার্টি শেষ হল, বাবামশায় নিজে দাঁড়িয়ে সকলের খোঁজখবর নিয়ে সব ব্যবস্থা করে অতিথি-অভ্যাগত আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব সকলকে হাসিমুখে বিদায় দিলেন। অন্দর-মহলে মা পিসিমা ব্যস্ত আছেন জামাইষষ্টীর তত্ত্ব পাঠাতে।
এমন সময়ে খবর হল বাবামশায়ের অসুখ। এত হৈ-চৈ হতে হতে কেমন একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্কের ছায়া পড়ল সবার মুখে চোখে চলায় বলায়। পিসেমশাইরা ছুটলেন ওষুধ আনতে, ডাক্তার ডাকতে; নীলমাধববাবু হাঁকছেন, ‘বরফ আন্, বরফ আন্।’ দাসদাসীরা গুজগুজ ফিসফাস করছে এখানে ওখানে। জ্যৈষ্ঠ মাস, ঝড়ের মেঘ উঠল কালো হয়ে, শোঁ-শোঁ বাতাস বইল। ভোরের বেলা পিসীরা আমাদের ঠেলে তুলে দিলে, ‘যা শেষ দেখা দেখে আয়।’ নিয়ে গেল আমাদের বাবামশায়ের ঘরে। বিছানায় তিনি ছট্ফট্ করছেন। পাশ থেকে কে একজন বললেন, ‘ছেলেদের দেখতে চেয়েছিলে। ছেলেরা এসেছে দেখ।’ শুনে বাবামশায় ঘাড় একটু তুলে একবার তাকালেন আমাদের দিকে, তারপর মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মাথা কাত হয়ে পড়ল বালিশে । বড়পিসিমা ছোটপিসিমা চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘এ কি, এ কি হল! কাল-জ্যৈষ্ঠ এল রে কাল-জ্যৈষ্ঠ।’
সেইদিন থেকে ছেলেবেলাটা যেন ফুরিয়ে গেল।
০৭. তার পর গেল বেশ কিছুকাল
তার পর গেল বেশ কিছুকাল। একদিন বিয়ে হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে জীবনের ধরনধারণ ওঠাবসা সাজগোজ সব বদলে গেল। এখন উলটাে জামা পরে ধুলো পায়ে ছুটোছুটি করবার দিন চলে গেছে। চাকরবাকররা ‘ছোটবাবু মশায়’ বলে ডাকে, দরোয়ানরা ‘ছোট হুজুর’ বলে সেলাম করে। দু-বেলা কাপড় ছাড়া অভ্যেস করতে হল, শিমলের কোঁচানো ধুতি পরে ফিটফাট হয়ে গাড়ি চড়ে বেড়াতে যেতে হল, একটু আধটু আতর ল্যাভেণ্ডার গোলাপও মাখতে হল, তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসতে হল, গুড়গুড়ি টানতে হল, ড্রেসসুট বুট এঁটে থিয়েটার যেতে হল, ডিনার খেতে হল, এককথায় আমাদের বাড়ির ছোটবাবু সাজতে হল।
বাল্যকালটাতে শিশুমন কি সংগ্রহ করলে তা তো বলে চুকেছি অনেকবার অনেক জায়গায়, অনেকের কাছে। যৌবনকালের যেটুকু সঞ্চয় মন-ভোমরা করে গেছে তার একটু একটু স্বাদ ধরে দিয়েছি, এখনো দিয়ে চলেছি হাতের আঁকা ছবির পর ছবিতে। এ কি বোঝো না? পদ্মপত্রে জলবিন্দুর মত সে সব সুখের দিন গেল। তার স্বাদ পাওনি কি ওই নামের ছবিতে আমার। প্রসাধনের বেলায় জোড়াসাঁকোর বাড়িতে অন্দরমহলে যে সুন্দর মুখ সব, যে ছবি সব সংগ্রহ করলে মন, আমার ‘কনে সাজানো’ ছবিখানিতে তার অনেকখানি পাবে। সুখের স্বপ্ন ভাঙানো যে দাহ সেও সঞ্চিত ছিল মনে অনেকদিন আগে থেকে। সুখের নীড়ে বাসা করেছিলেম, তবেই তো আঁকতে শিখে সে মনের সঞ্চয় ধরেছি ‘সাজাহানের মৃত্যুশয্যা’ ছবিতে।
বাল্যে পুতুল খেলার বয়সের সঞ্চয় এই শেষবয়সের যাত্রাগানে, লেখায়, টুকিটাকি ইঁটকাঠ কুড়িয়ে পুতুল গড়ায় যে ধরে যাচ্ছিনে তা ভেবে না। সেই বাল্যকাল থেকে মন সঞ্চয় করে এসেছে। তখনই যে সে সব সঞ্চয় কাজে লাগাতে পেরেছিলেম তা নয়। ধরা ছিল মনে। কালে কালে সে সঞ্চয় কাজে এল; আমার লেখার কাজে, ছবি আঁকার কাজে, গল্প বলার কাজে, এমনি কত কি কাজে তার ঠিক নেই। এই নিয়মে আমার জীবনযাত্রা চলেছে। আমার সঞ্চয়ী মন। সঞ্চয়ী মনের কাজই এই—সঞ্চয় করে চলা, ভালো মন্দ টুকিটাকি কত কি! কাক যেমন অনেক মূল্যবান জিনিস, ভাঙাচোরা অতি বাজে জিনিসও এক বাসায় ধরে দেয় মন-পাখিটিও আমার ঠিক সেইভাবে সংগ্রহ করে চলে যা-তা। সেই সব সংগ্রহ তুমি হিসেব করে গুছিয়ে লিখতে চাও লেখো, আমি বলে খালাস।
রোজ বেলা তিনটে ছিল মেয়েদের চুলবাঁধার বেলা। কবিত্ব করে বলতে হলে বলি, প্রসাধনের বেলা। আমাদের অন্দর ও রান্নাবাড়ির মাঝে লম্বা ঘরটায় বিছিয়ে দিত চাকরানীরা চুলবাঁধার আয়না মাদুর আরও নানা উপকরণ ঠিক সময়ে। মা পিসিমারা নিজের নিজের বউ ঝি নিয়ে বসতেন চুল বাঁধতে।
বিবিজি বলে এক গহনাওয়ালী হাজির হত সেই সময়ে—কোন্ নতুন বউয়ের কানের মুক্তোর দুল চাই, কোন মেয়ের নাকের নাকছাবি চাই, খোঁপায় সোনারুপোর ফুল চাই, তাই জোগাত। চুড়িওয়ালী এসে ঝুড়ি খুলতেই তুলতুলে হাত সব নিসপিস করত চুড়ি পরতে। ছোট ছোট রাংতা দেওয়া গালার চুড়ি, কাঁচের চুড়ি, কত কৌশলে হাতে পরিয়ে দিয়ে চলে যেত সে পয়সা নিয়ে। চুড়ি বেচবার কৌশলও জানত। চুড়ি পরাবার কৌশলও জানত। কোন্ রঙের পর কোন্ চুড়ি মানাবে বড় চিত্রকরীর মত বুঝত তার হিসেব সেই চুড়িওয়ালী। বোষ্টমী আসত ঠিক সেই সময়ে ভক্তিতত্ত্বের গান শোনাতে। তোমরা বঙ্কিমবাবুর নভেলে যে সব ছবি পাও সে সব ছবি স্বচক্ষে দেখেছি আমি খুব ছেলেবেলায়। এখনো চুড়ি পরানো ছবি আঁকতে সেই শিশুমনের সংগ্ৰহ কাজ দেয়। হাতের চুড়িগুলি আঁকতে কোন্ রঙের পর কোন্ রঙের টান দিতে হবে জানি, সেজন্য আর ভাবতে হয় না। তুমি যে সেদিন বললে, সাঁওতালনীদের খোঁপা আপনি কেমন করে ঠিকটি এঁকে দিলেন? খোঁপার কত রকম প্যাঁচ সেই চুল বাঁধার ঘরে বসে শিশুদৃষ্টি শিশুমন ধরেছিল।
মা বসে আছেন কাঠের তক্তপোশে, দাসীরা চুল বেঁধে দিচ্ছে ছোট ছোট বউ-মেয়েদের। সে কত রকমের চুল বাঁধার কায়দা খোঁপার ছাঁদ। বোষ্টমী বসে গাইত, ‘কানড়া ছান্দে কবরী বান্ধে।’ সেই কানড়া ছান্দের খোঁপা বাঁধত বসে পাড়াগাঁয়ের দাসীরা। তোমরা খোঁপা তো বাঁধো, জানো সে খোঁপা কেমন? মোচা খোঁপা, কলা খোঁপ, বিবিয়ানা খোঁপা, পৈচে ফাঁস, মনধরা খোঁপার ফাঁস, কত তার বর্ণনা দেব। কত বা এঁকে দেখাব। এইবার আসত ফুলওয়ালী কলাপাতার মোড়কে ফুলমালা হাতে। সেই ফুলমালা নিজের হাতে জড়িয়ে দিতেন মা খোঁপায় খোঁপায়। সন্ধ্যেতারা উঠে যেত, চাঁদ উঠে যেত। সন্ধ্যে হ’লই গোঁপে তা দিয়ে দক্ষিণের বারান্দায় বসে আলসেমি করি—মতিবাবু আসেন, শ্যামসুন্দর আসেন। আমি বসি কোনোদিন ম্যাণ্ডোলিন নিয়ে, কোনোদিন বা এসরাজ নিয়ে। মতিবাবু শিবের বিয়ের পাঁচালি গান—
তোরা কেউ যাসনে ওলো ধরতে কুলো কুলবালা, মহেশের ভূতের হাটে এসব ঠাটে সন্ধ্যেবেলা।
যেরূপ ধরেছিস তোরা, চিত-উন্মত্ত-করা,
চাঁদ যেন ধরায় ধরা, খোঁপায় ঘেরা বকুলমালা।
এই রকম বকুলমালা জুইমালায় সাজানো সে-বয়েসের দিনরাতগুলো আনন্দে কাটে। মা রয়েছেন মাথার উপরে, নির্ভাবনায় আছি।
ভুবনবাই বলে একটা বুড়ি আসত। মা তাকে বউদের গান শোনাতে বলতেন। সখীসংবাদ, মাথুর, গাইত সে এককালে আমার ছোটদাদামশায়ের আমলে—
তোরা যাসনে যাসনে যাসনে, দূতী
গেলে কথা কবে না সে নব ভূপতি।
যদি যাবি মধুপুরে
আমার কথা কোসনে তারে।
বৃন্দে, তোর ধরি করে, রাখ এ মিনতি।
ফোকলা দাঁতে তোতলা তোতলা সুরে সে এই গান গেয়ে মরেছে। কিন্তু সেই বুড়ি যেটুকখানি ধরে গেছে আমার মনে, সেই বস্তুটুকুও যে আমার কৃষ্ণলীলার কোনো ছবিতে নেই তা মনে কোরো না।
নান্নীবাই শুনেছি এককালে লক্ষ্ণৌএর খুব নামকরা বাইজি ছিল, রুপোর খাটে শুত, এত ঐশ্বর্য। সর্বস্ব খুইয়ে সে আসে ভিখিরির মতো, পাঁচিলঘেরা গোল চক্করের কাছে বসে গান গায়, এবাড়ি ওবাড়ি থেকে কিছু টাকাপয়সা যা পায় নিয়ে চলে যায়। বুড়োবয়েসেও চমৎকার গলা ছিল তার, এখনকার অনেক ওস্তাদ হার মেনে যায়।
শ্রীজানও আসে। সেও বুড়ো হয়ে গেছে। চমৎকার গাইতে পারে। মাকে বললুম, ‘মা, একদিন ওর গান শুনব।’ মা বললেন শ্ৰীজানকে। সে বললে, ‘আর কি এখন তেমন গাইতে পারি। বাবুদের শোনাতুম গান, তখন গাইতে পারতুম। এখন ছেলেদের আসরে কি গাইব?’ মা বললেন, ‘তা হোক, একদিন গাও এসে, ওরা শুনতে চাইছে।’ শ্ৰীজান রাজি হল, একদিন সারারাতব্যাপী শ্ৰীজানের গানের জলসায় বন্ধুবান্ধবদের ডাক দেওয়া গেল। নাটোরও ছিলেন তার মধ্যে। বড় নাচঘরে গানের জলসা বসল। শ্ৰীজান গাইবে চার প্রহরে চারটি গান। শ্ৰীজান আরম্ভ করল গান। দেখতে সে সুন্দর ছিল না মোটেই, কিন্তু কী গলা, কোকিলকণ্ঠ যাকে বলে। এক-একটা গান শুনি আর আমাদের বিস্ময়ে কথা বন্ধ হয়ে যায়। চুপ করে বসে তিনটি গান শুনতে তিন প্রহর রাত্রি। এবারে শেষ প্রহরের গান। বাতিগুলো সব নিবে এসেছে, একটিমাত্র মিটমিট করে জ্বলছে উপরে। ঘরের দরজাগুলি বন্ধ, চারিদিক নিস্তব্ধ, যে যার জায়গায় আমরা স্থির হয়ে বসে। শ্ৰীজান ভোরাই ধরলে। গান শেষ হল, ঘরের শেষ বাতিটি নিবে গেল,—উষার আলো উঁকি দিল নাচঘরের মধ্যে। কানাড়া আর ভৈরবীতে শ্ৰীজান সিদ্ধ ছিল।
আর একবার গান শুনেছিলুম। তখন আমি দস্তুরমতো গানের চর্চা করি। কোথায় কে গাইয়ে-বাজিয়ে এল গেল সব খবর আসে আমার কাছে। কাশী থেকে এক বাইজি এসেছে, নাম সরস্বতী, চমৎকার গায়। শুনতে হবে। এক রাত্তিরে ছয়শো টাকা নেবে। শ্যামসুন্দরকে পাঠালুম, ‘যাও, দেখো কত কমে রাজি করাতে পারো।’ শ্যামসুন্দর গিয়ে অনেক বলে কয়ে তিনশো টাকায় রাজি করালে। শু্যামসুন্দর এসে বললে, ‘তিনশো টাকা তার গানের জন্য, আর দুটি বোতল ব্রাণ্ডি দিতে হবে।’ ব্রাণ্ডির নামে ভয় পেলেম, পাছে মার আপত্তি হয়। শ্যামসুন্দর বললে, ‘ব্রাণ্ডি না খেলে সে গাইতেই পারে না।’ তোড়জোড় সব ঠিক। সরস্বতী এল সভায়। স্থূলকায়া, নাকটি বড়িপানা, দেখেই চিত্তির। নাটোর বলেন, ‘অবনদা, করেছ কি। তিনশো টাকা জলে দিলে?’ দুটি গান গাইবে সরস্বতী। নাটোর মৃদঙ্গে সংগত করবেন বলে প্রস্তুত। দশটা বাজল, গান আরম্ভ হল। একটি গানে রাত এগারোটা । নাটোর মৃদঙ্গ কোলে নিয়ে স্থির। সরস্বতীর চমৎকার গলার স্বরে অত বড় নাচঘরটা রমরম করতে থাকল। কি স্বরসাধনাই করেছিল সরস্বতীবাই। আমরা সব কেউ তাকিয়া বুকে, কেউ বুকে হাত দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে। এক গানেই আসর মাত। গানের রেশে তখনও সবাই মগ্ন। সরস্বতীবাই বললে, ‘আউর কুছ ফরমাইয়ে।’ গান শুনে তাকে ফরমাশ করবার সাহস নেই কারো। এ ওর মুখের দিকে তাকাই। শেষে শ্যামসুন্দরকে বললুম, ‘একটা ভজন গাইতে বলো, কাশীর ভজন শুনেছি বিখ্যাত।’ সে একটি সকলের জানা ভজন গাইলে, ‘আও তো ব্ৰজচন্দ্রলাল।’ সব স্তম্ভিত। আমি তাড়াতাড়ি তার ছবি আঁকলুম, পাশে গানটিও লিখে রাখলুম। গান শেষ হল, সে উঠে পড়ল। দুখানা গানের জন্য তিনশো টাকা দেওয়া যেন সার্থক মনে হল।
এমনিতরো নাচও দেখেছিলুম সে আর-একবার। নাটােরের ছেলের বিয়ে, নাচগানের বিরাট আয়োজন। কর্ণাট থেকে নামকরা বাইজি আনিয়েছেন। খুব ওস্তাদ নাচিয়ে মেয়েটি। এসেছে তার দিদিমার সঙ্গে। বুড়ী দিদিমা কালকাবিন্দের শিষ্যা। সভায় বসেছে সবাই। বুড়িটির সঙ্গে নাতনিটিও ঢুকলো; বুড়ি পিছনে বসে রইল, মেয়েটি নাচলে। চমৎকার নাচলে, নাচ শেষ হতে চারদিকে বাহবা রব উঠল। আমার কি খেয়াল হল ওই বুড়িটির নাচ দেখব। নাটোর শুনে বললেন, “অবনদা, তোমার এ কি পছন্দ।’ বললুম, ‘তা হোক, শখ হয়েছে বুড়ির নাচ দেখবার। তুমি তাকে বলো, নিশ্চয়ই এই বুড়ি খুব চমৎকার নাচে।’ নাটোর বুড়িকে বলে পাঠালে। বুড়ি প্রথমটায় আপত্তি করলে, সে বুড়ো হয়ে গেছে, সাজসজ্জাও কিছু আনেনি সঙ্গে। বললুম, কোনো দরকার নেই, তুমি বিনা সাজেই নাচো। বুড়ি নাতনিকে নিয়ে ভিতরে গেল—ওদের নিয়ম, সভায় এক নাচিয়ে উপস্থিত থাকলে আর একজন নাচে না। খানিক পরে বুড়ি নাতনির পাঁয়জোর পরে উড়নিটি গায়ে জড়িয়ে সভায় ঢুকল। একজন সারেঙ্গিতে সুর ধরলে। বুড়ি সারেঙ্গির সঙ্গে নাচ আরম্ভ করলে। বলব কি, সে কি নাচ! এমনভাবে মাটিতে পা ফেলল, মনে হল, যেন কার্পেট ছেড়ে দু-তিন আঙুল উপরে হাওয়াতে পা ভেসে চলেছে তার। অদ্ভুত পায়ে চলার কায়দা; আর কি ধীর গতি। জলের উপর দিয়ে হাঁটল কি হাওয়ার উপর দিয়ে বােঝা দায়। বুড়ির বুড়ো মুখ ভুলে গেলুম, নৃত্যের সৌন্দর্য তাকে সুন্দরী করে দেখালে।
আর-একবার ব্লান্ট সাহেব, উডরফ সাহেব, আমরা কয়েকজন দেশী সংগীতের অনুরাগী মিলে মাদ্রাজ থেকে একজন বীনকারকে আনিয়েছিলুম। সপ্তাহে সপ্তাহে রাত নটার পরে আমাদের বাড়িতে সেই বীনকারের বৈঠক বসত। সাহেবসুবাদের জন্য থাকত কমললেবুর শরবত, আইসক্রীম, পান-চুরুটের ব্যবস্থা। রাত্তিরে শহরের গোলমাল যখন থেমে আসত, বাড়ির শিশুরা ঘুমিয়ে পড়ত, চাকরদের কাজকর্ম সারা হত, চারদিক শান্ত, তখন বীণা উঠত বীনকারের হাতে। কাইজারলিঙও একবার এলেন সেই আসরে। বীনকার বীণা বাজিয়ে চলেছে, পাশে কাইজারলিঙ স্থির হয়ে চোখ বুজে ব’সে, চেয়ে দেখি বাজনা শুনতে শুনতে তার কান গাল লাল টকটকে হয়ে উঠল। স্বরের ঠিক রংটি ধরল সাহেবের মনে। ঝাড়া একটি ঘণ্টা পূর্ণচন্দ্রিকা রাগিণীটি বাজিয়ে বীনকার বীন রাখলে। মজলিস ভেঙে আর কারো মুখে কথা নেই, আস্তে আস্তে সব যে যার বাড়ি ফিরে গেলেন।
০৮. জোড়াসাঁকোর বাড়ির দোতলা
জোড়াসাঁকোর বাড়ির দোতলার দক্ষিণের বারান্দা—পুরুষানুক্রমে আমাদের আমদরবার, বসবার জায়গা; প্রকাণ্ড বারান্দা, পুব থেকে পশ্চিমে বাড়িসমান লম্বা দৌড়। তারই এক-এক খাটালে এক-একজনের বসবার চৌকি, সে চৌকি নড়াবার জো ছিল না। ঈশ্বরবাবুর এক, নবীনবাবুর এক, ছোটপিসেমশায়ের এক, বড়পিসেমশায়ের এক, নগেনবাবুর এক, কালাচাঁদবাবুর এক, অক্ষয়বাবুর এক, বৈকুণ্ঠবাবুর এক, বাবামশায়ের এক—এমনি সারি সারি চৌকি দুদিকে। এঁরা সকলেই এক-এক চরিত্র, এঁরা অনেকে বাইরের হয়েও একেবারে জোড়াসাঁকোর ঘরের মত ছিলেন। বাবামশায়ের পোষা কাকাতুয়ার পর্যন্ত একটা খাটাল ছিল, দেয়ালে নিজের স্থান দখল করে বসে থাকত, সেও যেন এক সভাসদ্। সকাল-বিকেল আড্ডার জায়গা ছিল ওই বারান্দা, চিরকাল দেখে এসেছি। গুড়গুড়ি ফরসি হুঁকো বৈঠকে সাজিয়ে দিত চাকররা। কাছারির কাজও চলত সেখানে, দেওয়ান আসত, আসত বয়স্য, পারিষদ। গান, খোসগল্প, হাসি কত কী হত। দেখেছি, ঈশ্বরবাবু নবীনবাবু ওঁরা যে যার জায়গায় হুঁকো খাচ্ছেন, বাবামশায় আছেন ইজিচেয়ারে বসে, ড্রইং বোর্ড কোলে প্ল্যান আঁকছেন। বারান্দায় জোড়া জোড়া থাম, তার মাঝে মাঝে বড় বড় খাটাল, পুবধারে একটা বড় খিলেন, পশ্চিমধারে তেমনি আর-একটা সত্তর-আশি ফুট লম্বা, চওড়াও অনেকটা।
ঈশ্বরবাবু আসতেন রোজ সকালে লাঠি ঠকাস ঠকাস করতে করতে। হাতে রুমালে বাঁধা কচি আম, কোনোদিন বা আর কিছু, যা নতুন বাজারে উঠেছে। বাজারে যে ঋতুতে যা কিছু নতুন উঠবে এনে দিতে হবে, এই ছিল তার সঙ্গে বাবামশায়ের কথা।
নিত্য যাঁরা আসতেন আমদরবারে, তাঁদের কথা তো বলেইছি, অন্যরা কেউ এলে তাঁদেরও বসানো হত ওখানেই। আপিস যাবার আগে পর্যন্ত দক্ষিণের বারান্দায় তাঁদের দরবার বসত। তার পর দক্ষিণের বারান্দা খালি—যে যার বাড়ি চলে গেলেন, বাবামশায় উঠে এলেন, বিশ্বেশ্বর ফরসি গুড়গুড়ি তুলে নিলো। আমরা তখন ঢুকতুম সেখানে; নবীনবাবু হয়তো তখনও বসে আছেন, তাঁকে ধরতুম ফ্যান্সি ফেয়ারে নিয়ে যেতে হবে, ইডেন গার্ডেনে বেড়িয়ে আনতে হবে। বাবামশায়ের দরবারে আমাদের দরখাস্ত পেশ করতে হবে, তিনি হুকুম দেবেন তবে যেতে পারব। আমাদের হয়ে নবীনবাবুই সে কাজটা করতেন।
পুজোর সময় দক্ষিণের বারান্দায় কত রকমের ভিড়। চীনেম্যান এল, জুতোর মাপ দিতে হবে। আমাদের ডাক পড়ত তখন দক্ষিণের বারান্দায়। খবরের কাগজ ভাঁজ করে সরু ফিতের মত বানিয়ে চীনেম্যান পায়ের মাপ নিত, এখনও তার আঙুলগুলো দেখতে পাচ্ছি। দরজি এল, ঈশ্বরবাবু হাঁকলেন, ‘ওহে, ওস্তাগর এসেছে, এসো এসো ভাইসব, মাপ দিতে হবে গায়ের।’ ফিতে খুলে দাঁড়িয়ে দরজি, মোটা পেট, গায়ে সাদা জামা, মাথায় গম্বুজের মত টুপি, সে আমাদের পুতুলের মত ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মাপ নিয়ে ছেড়ে দিতে ঈশ্বরবাবুও উঠে এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন, ‘আমারও গায়ের মাপটা নিয়ে নাও, একটা সদ্রী—পুজো আসছে’ বলে বাবামশায়ের দিকে তাকান। বড়বাজারের পাঞ্জাবী শালওয়ালা বসে আছে নানারকম জরির ফুল দেওয়া ছিট, কিংখাবের বস্তা খুলে। বাবামশায়ের পছন্দমত কাপড় কাটা হলে অমনি নবীনবাবু বলতেন, ‘বাবা, আমার নলিনেরও একটা চাপকান হয়ে যাক এই সঙ্গে।’
আতরওয়ালা এসে হাজির, গেব্রিয়েল সাহেব, আমরা বলতুম তাকে গিব্রেল সাহেব—একেবারে খাস ইহুদি—যেন শেক্সপিয়রের মাৰ্চেণ্ট অব ভেনিসের শাইলকের ছবি জ্যান্ত হয়ে নেমে এসেছে জোড়াসাঁকোর দক্ষিণের বারান্দায় ইস্তাম্বুল আতর বেচতে—হুবহু ঠিক তেমনি সাজ, তেমনি চেহারা। গিব্রেল সাহেবের ঢিলে আচকান, হাতকাটা আস্তিন, সরু সরু একসার বোতাম ঝিক ঝিক করছে; ঔরঙ্গজেবের ছবিতে এঁকে দিয়েছি সেরকম। সে আতর বেচতে এলেই ঈশ্বরবাবু অক্ষয়বাবু সবাই একে একে খড়কেতে একটু তুলো জড়িয়ে বলতেন, ‘দেখি দেখি, কেমন আতর’ বলে আতরে ডুবিয়ে কানে গুঁজতেন। পুজোর সময় আমাদের বরাদ্দ ছিল নতুন কাপড়, সিল্কের রুমাল। সেই রুমালে টাকা বেঁধে রমানাথ ঠাকুরের বাড়িতে পুজোর সময় যাত্রাগানে প্যালা দিতুম। বলিনি বুঝি সে গল্প? হবে, সব হবে, সব বলে যাব আস্তে আস্তে। নন্দফরাশের ফরাশখানার মত পুরোনো গুদোমঘর বয়ে বেড়াচ্ছি মনে। কত কালের কত জিনিসে ভরা সে ঘর, ভাঙাচোড়া দামি অদামিতে ঠাসা। যত পারো নিয়ে যাও এবারে—হালকা হতে পারলে আমিও যে বাঁচি। হ্যাঁ, সেই সিল্কের রুমাল গিব্রেল সাহেবই এনে দিত। আর ছিল বরাদ্দ সকলের ছোট ছোট এক-এক শিশি আতর।
কতরকম লোক আসত, কত রকম কাণ্ড হত ওই বারান্দায়। একবার মাইক্রসকোপ এসেছে বিলেত থেকে, প্যাকিং বাক্স খোলা হচ্ছে। কি ঘাস দিয়ে যেন তারা প্যাক করে দিয়েছে, বাক্স খোলা মাত্র বারান্দা সুগন্ধে ভরপুর। ‘কি ঘাস, কি ঘাস’, বলে মুঠো মুঠো ঘাস ওখানে যারা ছিলেন সবাই পকেটে পুরলেন, বাড়ির ভিতরেও গেল কিছু, মেয়েদের মাথা ঘষার মসলা হবে। মাইক্রসকোপ রইল পড়ে, ঘাস নিয়েই মাতামাতি, দেখতে দেখতে সব ঘাস গেল উড়ে। আমিও এক ফাঁকে একটু নিলুম, বহুদিন অবধি পকেটে থাকত হাতের মুঠোয় নিয়ে গন্ধ শুঁকতুম।
তার পর আর একবার এল ওই বারান্দায় এক রাক্ষস, কাঁচা মাংস খাবে। সকাল থেকে যদু মাস্টার ব্যস্ত, আমাদের ছুটি দিয়ে দিলেন রাক্ষস দেখতে। ‘দেখবি আয়, দেখবি আয়, রাক্ষস এসেছে’ বলে ছেলের দল গিয়ে জুটলুম সেখানে । মা পিসিমারাও দেখছেন আড়ালে থেকে খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে। ছেলে বুড়ো সবাই সমান কৌতুহলী। রাবণের গল্প পড়েছি, সেই দেশেরই রাক্ষস, কৌতুহল হচ্ছে দেখতে, আবার ভয়-ভয়ও করছে। ‘এসেছে, এসেছে, আসছে, আসছে’ রব পড়ে গেল। বাবামশায়ের পোষা খরগোস চরে বেড়াচ্ছে বারান্দায়—কেদারদা চেঁচিয়ে উঠলেন, খরগোসগুলিকে নিয়ে যা এখান থেকে, রাক্ষস খেয়ে ফেলবে।’ শুনে আমরা আরো ভীত হচ্ছি, না জানি কি। খানিক পরে রাক্ষস এলো, মানুষ—বিশ্বেশ্বরের মতই দেখতে রোগাপটকা অতি ভালোমানুষ চেহারা—দেখে আমি একেবারে হতাশ। চাকররা একটা বড় গয়েশ্বরী থালাতে গোটা একটা পাঁঠা কেটে টুকরো টুকরো করে নিয়ে এল রান্নাঘর থেকে। সেই মাংসের নৈবেদ্য সামনে দিতেই খানিকটা নুন মেখে লোকটা হাপ্ হাপ্ করে সব মাংস খেয়ে টাকা নিয়ে চলে গেল। সেই এক রাক্ষস দেখেছিলেম ছেলেবেলায়, কাঁচাখোর।
সেকালের লোকদের ছোট বড় সবারই এক-একটা চরিত্র থাকত। অক্ষয়বাবু আসতেন ফিটফাট বাবুটি সেজে। তার কথা তো অনেক বলেছি আগের সব গল্পে। সে সময়ে ফ্যাশান বেরিয়েছে বুকে মড়মড়ে পেলেট দেওয়া চোস্ত ইস্তিরি করা শার্ট, তাই গায়ে দিয়ে এসেছেন অক্ষয়বাবু। কালো রঙ ছিল তার, বাবরি চুল, গোঁফে তা, কড়ে আঙুলে একটা আংটি। গানও গাইতেন মাঝে মাঝে, খুব দরাজ গলা ছিল। গান কিছু বড় মনে নেই, সুরটাই আছে কানে এখনও বড় বড় রাগরাগিণীর—আমি তখন কতটুকুই বা, ছয়-সাত বছর বয়স হবে আমার। এখন, অক্ষয়বাবু তো বসে আছেন চৌকিতে সেই নতুন ফ্যাশানের পেলেট দেওয়া শার্ট গায়ে দিয়ে। আমি কাছে গিয়ে অক্ষয়বাবুর বুকের মড়মড়ে পেলেটে হাত বোলাতে বোলাতে বললুম, “অক্ষয়বাবু এ যে শার্সি খড়খড়ি লাগিয়ে এসেছেন।’ যেমন বলা বারান্দাসুদ্ধ সকলের হো-হো হাসি, ‘শার্সি খড়খড়ি’। হাসি শুনে ভাবলুম কি জানি একটা অপরাধ করে ফেলেছি। চোঁচাঁ দৌড় সেখান থেকে। বিকেলে আবার শুনি, সেই আমার ‘শার্সি খড়খড়ি’ পরার কথা নিয়ে হাসি হচ্ছে সবাইকার।
দরজি চীনাম্যান, তারাও এক-একটা টাইপ, তাই চোখের সামনে স্পষ্ট তাদের দেখতে পাই এখনো। ঈশ্বরবাবু শিখিয়ে দিয়েছিলেন চীনে ভাষা, ইরেন দে পাগলা, উড়েন দে পাগলা, কা সে।’ ভাবটা বোধ হয়, জুতো এ পায়েও গলাই ও পায়েও গলাই, দুপায়েই লাগে কষা। চীনাম্যান এলেই আমরা চীনেম্যানকে ঘিরে ঘিরে ওই চীনে ভাষা বলতুম, আর সে হাসত। ঢিলেঢালা পাজামা, কালো চায়নাকোট গায়ে, ঠিক তার মতই টাক-টিকিতে সেজে এক চীনেম্যানরূপে বেরিয়েছিলুম ‘এমন কার্য আর করব না’ প্রহসনে।
শ্ৰীকণ্ঠবাবু আসতেন। এই এখানকার রায়পুর থেকে যেতেন মাঝে মাঝে কলকাতায় কর্তামশায়ের কাছে। বুড়োর চেহারা মনে আছে, পাকা আমটির মত গায়ের রঙ, জরির টুপি মাথায়। গাইতেন চৌকিতে বসে ‘ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্’ আর ‘পুণ্যপুঞ্জেন যদি প্রেমধনং কোঽপি লভেৎ’। আমরাও দুহাত তুলে গাইতুম, ‘কোঽপি লভেৎ কোঽপি লভেৎ’। সেদিন শুনলুম ৭ই পৌষে ছাতিম তলায় এই গান। শুনেই মনে হল শ্ৰীকণ্ঠবাবুর মুখে ছেলেবেলায় শেখা গান। ষাট-সত্তর বছর পরে এই গান শুনে মনে পড়ে গেল সেই দক্ষিণের বারান্দায় শ্ৰীকণ্ঠবাবু গাইছেন, আমরা নাচছি। ছোট্ট একটি সেতার থাকত সঙ্গে, সেইটি বাজিয়ে আমাদের নাচাতেন। বড় ভালোবাসতেন তিনি ছোট ছেলেদের। কর্তা মশায়ের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব ছিল। তারই বাড়িতে আসতে মাঝপথে তিনি বিশ্রাম নিতেন ওই ছাতিমতলায়। স্টেশন থেকে পালকি করে এসে এইখানে নেমে বিশ্রাম নিয়ে তবে যেতেন রায়পুর সিংহিদের বাড়ি। বড় ভালো লেগেছিল কর্তামশায়ের ছাতিমতলাটি। তাই তিনি এখানে নিজের একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করবার কল্পনা করেছিলেন। এ সমস্তই ছিল তখন শ্ৰীকণ্ঠবাবুর দখলে।
তখনকার দিনে গুরুজনদের মান কি দেখতুম। আমদরবার বসেছে, খবর এল, কালীকৃষ্ণ ঠাকুর পাথুরেঘাটা থেকে দেখা করতে আসছেন। শুনে কি ব্যস্ত সবাই। তোল্ তোল্ হুঁকো কলকে সব তোল্, সরা এখান থেকে এসব। বাবামশায় ঢুকলেন ঘরে, পরিষ্কার জামাকাপড় পরে তৈরি। গুরুজন আসছেন, ভালোমানুষ সেজে সবাই অপেক্ষা করতে লাগলেন। ছোট ছেলেদের মত গুরুজনকে ভয় করতেন তাঁরা; গুরুজনরা এলে সমীহ করা, এটা ছিল। কর্তামশায় এসেছিলেন, বলেছি তো সে গল্প—তাড়াহুড়ো, দেউড়ি থেকে উপর পর্যন্ত ঝাড়পোঁছ, যেন বর আসছেন বাড়িতে।
জোড়াসাঁকোর বাড়ির দক্ষিণ বারান্দার আবহাওয়া, এ যে কি জিনিস! সেই আবহাওয়াতেই মানুষ আমরা। এবাড়ির যেমন দক্ষিণের বারান্দা ওবাড়িরও তেমনি দক্ষিণের বারান্দা। পিসিমাদের মুখে শুনতুম ওবাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় বিকেলে দাদামশায়ের বৈঠক বসত। যখন-তখন জুঁই আর বেলফুলের সুগন্ধে সমস্ত বাড়ি পাড়া তর্ হয়ে যেত। দাদামশায়ের শখ, বসে বসে ব্যাটারি চালাতেন। জলে টাকা ফেলে দিয়ে তুলতে বলতেন। একবার এক কাবুলিকে ঠকিয়েছিলেন এই করে। জলে টাকা ফেলে ব্যাটারি চার্জ করে দিলেন। কাবুলি টাকা তুলতে চায়, হাত ঘুরে এদিকে ওদিকে বেঁকে যায়, টাকা আর ধরতে পারে না কিছুতেই। তার পর জ্যেঠামশায়ের আমলে তিনি বসলেন সেখানে। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, বড় বড় পণ্ডিত ফিলজফার আসতেন। স্বপ্নপ্রয়াণ পড়া হবে, এ বারান্দা থেকে ছুটলেন বাবামশায়রা সে বারান্দায়। থেকে থেকে জ্যেঠামশায়ের হাসির ধ্বনি পাড়া মাৎ করে দিত। সে হাসির ধুম আমরাও কানে শুনতুম।
তার পর আমাদের আমলে যখন বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় বৈঠক বসবার বয়স হল তখন সেকালের যাঁরা ছিলেন, মতিবাবু, অক্ষয়বাবু, ঈশ্বরবাবু, নবীনবাবু— আর দাদামশায়ের বৈঠকের একটি বুড়ো, কি মুখুজ্যে, নামটা মনে আসছে না, তাঁর ছবি আঁকা আছে, চেহারা গান গলার স্বর সব ধরা আছে মনে, নামটা এরি মধ্যে হারিয়ে গেল, তিনি গাইতেন—দাদামশায়ের বৈঠকখানায়, মাঝে মাঝে আমাদেরও গান শোনাতেন, দাদামশায়ের গল্প বলতেন—এই তিন কালের তিন-চারটি বুড়ো নিয়ে আমরা তিন ভাই বৈঠক জমালেম।
সেই দক্ষিণের বারান্দাতেই, ঠিক তেমনি হুঁকো কলকে ফরসি সাজিয়ে বসি। বাবামশায় যেখানে বসতেন সেখানে দাদা বসে ছবি আঁকেন, একটু তফাতে আমি বসি পুবের বড় খিলেনের ধারে, তার পর বসেন সমরদা। আমাদের বৈঠকেও সেইরকম শালওয়ালা আসে, নতুন নতুন বন্ধুবান্ধব আসে। সামনের বাগানে সেই সব গাছ; দাদামশায়ের হাতে পোঁতা নারকেলগাছ, কাঁঠালগাছ, বাবামশায়ের শখের বাগানে সেই ফোয়ারায় জল ছাড়ে, সেই ভাগবত মালী, সব দেখা যায় বারান্দায় বসে। বিকেলে পাথর-বাঁধানো গোল চাতালে বসি, কাঁচের ফরসিতে সেই গোলাপজলে গোলাপপাপড়ি মিশিয়ে তামাক টানি। কাল বদলেও যেন বদলায়নি, তিন পুরুষের আবহাওয়া খানিক খানিক বইছে তখনো দক্ষিণের বারান্দায়। ড্রামাটিক ক্লাবের শ্রাদ্ধ হবে, সেই বারান্দায় লম্বা ভোজের টেবিল পড়ল, লম্বা উর্দি পরে সেই নবীন বাবুর্চি, সেই বিশ্বেশ্বর হুঁকোবরদার দেখা দিল, সেই সব পুরানো ঝাড়লন্ঠনের বাতি জ্বলল, প্লেট গ্লাস সাজানো হল। তিন পুরুষের সেই সব গানের সুর এসে মেশে আবার নতুন নতুন গানের সঙ্গে, রবিকার গানের সঙ্গে, দ্বিজুবাবুর গানের সঙ্গে।
আরো হলে আমলে যখন আমরা আর্টিস্ট হয়ে উঠেছি, আর্ট সোসাইটির মেম্বর হয়েছি, বড় বড় সাহেবসুবো জজ ম্যাজিস্ট্রেট লাট আসেন বাড়িতে—কমলালেবুর শরবত, পানতামাক, বেলফুলে ভরে যায় সেই দক্ষিণের বারান্দা। বারান্দার পাশের বড় স্টুডিয়োতেই বীনকারের বীণা গভীর রাত্রে থেমে যায় সবাইকে স্তব্ধ করে দিয়ে। আবার যখন বাড়িতে কারো বিয়ে, লৌকিকতা পাঠাতে হয়, মেয়েরা থালা সাজিয়ে দেয়, সেই সওগাতের থালায় থালায় ভরে যায় সেই লম্বা বারান্দা।
তোমরা ভাবো, ঘরের ভিতরে স্টুডিয়োতে বসে ছবি আঁকতুম, তা নয়। বারান্দার এক দিকে আমি আর-একদিকে ছাত্ররা বসে যেত। মুসলমান ছাত্র আমার শমিউজমা একদিকে আসন পেতে বসে সারাদিন ছবি আঁকে, সন্ধ্যে হলে মক্কামুখো হয়ে নমাজ পড়ে নেয় ওই বারান্দাতেই। অবারিত দ্বার দক্ষিণের বারান্দায়, সবাই আসছে, বসছে, ছবি আঁকছি, গান চলছে, গল্পও হচ্ছে। এমনি করেই ছবি এঁকে অভ্যস্ত আমি। অবিনাশ পাগলা সেও আসে, কত রকম বুজরুকি দেখাতে লোক আনে। একদিন একটা লোক ফুঁ দিয়ে গোলাপের গন্ধ বাড়িময় ছড়িয়ে চলে গেল। বারান্দা যেন একটা জীবন্ত মিউজিয়াম। নানা চরিত্রের মানুষ দেখতে রাস্তায় বেরতে হত না, তার আপনিই উঠে আসত সেখানে।
পূর্ণ মুখুজ্যে, মাথায় চুল প্রায় ছিল না, চাঁচা ছোলা নাক-মুখের গড়ন। তিনি মারা যাচ্ছেন, মাকে বলে পাঠালেন, ‘মা, আমি গঙ্গাযাত্রা করব।’ মা আমাদের বললেন, ‘বন্দোবস্ত করে দে।’ আমরা বন্দোবস্ত করে দিলুম। মারা গেলে যেভাবে নিয়ে যায় সেইভাবে বাঁশের খাটিয়া এনে তাঁকে তাতে শুইয়ে নিয়ে চলল। তেতলায় থেকে মা’রা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন, দোতলার বারান্দা থেকে আমরাও দেখছি— বুড়ো খাটিয়ায় শুয়ে সজ্ঞানে চারদিকে তাকাতে তাকাতে চলেছে। উপরে মাকে দেখতে পেয়ে দু হাত জুড়ে প্রণাম জানালেন—ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিতে আমাদের জানালে, যাচ্ছি, ভাই সব। সরকার বরকার কাঁধে করে নিয়ে গেল তাকে ‘হরি বোল’ দিতে দিতে। এসবই দক্ষিণের বারান্দা থেকে দেখতুম, যেন বক্সে বসে এক-একটি সিন দেখছি। পরেশনাথের মিছিল গেল, বিয়ের শোভাযাত্রা গেল, আবার পূর্ণ মুখুজ্যেও গেল।
মতিবাবু, তার ছবি তো দেখছ, দাদা এঁকেছেন—চেয়ারের উপর পা তুলে বসে বুড়ো হুঁকো খাচ্ছেন। হুঁকো খেয়ে খেয়ে গোঁফ হয়ে গিয়েছিল সোনালি রঙের। সকালে হয় আর্টের কাজ, সন্ধ্যেয় আসর জমাই মতিবাবুকে নিয়ে, গানের চর্চা করি। আমি ম্যাণ্ডোলিন বা এসরাজ বাজাই, তিনি পাঁচালি বা শিবের বিয়ে গেয়ে চলেন। বড় সরেশ লোক ছিলেন। ছেলের বিয়েতে আটচালা বাঁধতে হবে, মতিবাবু ছাড়া আর কেউ সে কাজ পারবে না। শহরের কোথায় কোথায় ঘুরে কাকে কাকে ধরে নকশামাফিক আটচালা বাঁধাবেন একপাশে বসে বুড়ো তামাক টানতে টানতে। এই মতিবাবু মরবার পরও দেখা দিয়েছিলেন, সে এক আশ্চর্য গল্প।
মতিবাবুর একবার দুরন্ত অসুখ। ছেলে এসে বললে, আর বাঁচবেন না। দেশে নিয়ে গেল। খবরাখবর নেই, ভাবছি কি হল তাঁর। অনেকদিন পরে একদিন ফিরে এলেন, দিব্যি ফিটফাট লাল চেহারা নিয়ে। বললুম, ‘এমন সুন্দর চেহারা হল কি করে? মনেই হয় না যে অসুখে ভুগে উঠেছেন।’ তিনি বললেন, ‘না, এবার তো সেরে ওঠবার কথাই ছিল না। অসুখে ভুগছি, ডাক্তার-কবিরাজের ওষুধ খাচ্ছি। কিছুতেই কিছু না। শেষে একদিন গাঁয়ের এক মৌলবী বললে, ঠাকুর, ও ওষুধপত্রে কিছু হবে না। আমার একটি ওষুধ খাবেন? একটু করে সুরুয়া বানিয়ে এনে দেব রোজ। কতদিন যাবৎ ভুগছি, মৌলবীর কথাতেই রাজি হলেম। সেই সুরুয়া খেতে খেতেই দেখুন চেহারা কি রকম বদলে গেল।’ বললুম, ‘ভালোই তো, তা এখনো একটু একটু সুরুয়া চলুক না, তৈরি করে দেবে বাবুর্চি।’ তিনি বললেন, ‘না, আর দরকার হবে না।’ দিব্যি রইলেন সে যাত্রা। তার পর সত্যিই যেবার ডাক পড়ল সেই যে গেলেন আর এলেন না। সেবারেও তিনি অসুখে পড়লেন। বড় ছেলে এসে নিয়ে গেল তাঁকে দেশে, একরকম জোর করেই। অনেকদিন আর কোনো খবর পাইনে, ভাবছি, এবারও বুঝি আগের মতই হঠাৎ একদিন এসে উপস্থিত হবেন। সকালে বসে আছি বারান্দায়, একটা লোক ধীরে ধীরে এসে বাগানে ঢুকল, দেখি মতিবাবু। চাকরদের বললুম, ‘ওরে দেখ্ দেখ্, মতিবাবু আসছেন, তামাক টামাক ঠিক রাখ্।’ চাকররা ছুটে নেমে গেল নিচে, দেখলে কোথাও কেউ নেই। বললুম, ‘আমি নিজের চোখে স্পষ্ট দেখলুম দিনের বেলা, তিনি বাগান দিয়ে হেঁটে দেউড়িতে আসছেন। নিশ্চয়ই তিনি হবেন, খুঁজে দেখ্, যাবেন কোথায় আর।’ কিন্তু তাঁকে আর পাওয়া গেল না খুঁজে। দু-চারদিন বাদে তাঁর ছেলে এসে জানালে মতিবাবুর গঙ্গালাভ হয়েছে। ভাবি, তারও কি এমনি টান ছিল তবে ওই বারান্দার উপর।
দক্ষিণের বারান্দার মায়া, কি বুড়ো কি ছেলে, কেউ ছাড়তে পারেনি। ঈশ্বরবাবু আসতেন, ছেলেবেলায় দ্বারকানাথের আমলের জাহাজের মত প্রকাণ্ড একটা কৌচে বসে তাঁর কাছে সন্ধ্যেবেলায় গল্প শুনেছি সেকালের কর্তাদের। ঠিক সেই জায়গায় তাঁর সেই চৌকি থাকবে, একটু নাড়ালে উস্খুস করতেন। আমরা কোনো কোনো দিন দুষ্টুমি করে সে জায়গা দখল করলে বলতেন, ‘ভাই, আমার জায়গাতে কেন?’ অন্য কোনও চৌকি তার পছন্দ নয়। নিজের চৌকিতে ‘আঃ’ বলে বসে পড়তেন, সে যে কত আরামের ‘আঃ’। আসতে যেতে বাগানের লম্বা ঘাসে পা পুঁছে আসতেন, সেই ছিল তার পাপোশ। সেই ঈশ্বরবাবু অসুখে পড়লেন। আশি বছরে চোখ কাটালেন, চোখ ভালো হল, খবরের কাগজ পড়লেন। একদিন বললেন, ‘জানো ভাই? আমার একটা কষের দাঁত উঠছে।’ কুষ্টি পেরিয়ে গেছে, ভারি ফুর্তি। নবীনবাবুর বাড়িতে পড়ে আছেন। মাঝে মাঝে যাই, তাঁকে দেখে আসি। তিনি বলেন, ‘ভালো আছি, ভাই, এই কালই গিয়ে বসব তোমাদের বারান্দায়।’ শেষ দিনও বলেছিলেন ‘কালই যাব সেখানে’; আর ঈশ্বরবাবুর আসতে হল না।
পূৰ্ণবাবুর মত ঈশ্বরবাবুকে নিয়ে গেল, দেখলুম দক্ষিণের বারান্দায় দাঁড়িয়ে। তাঁর বাশের লাঠিটি আমায় দিয়ে গিয়েছিলেন। পুরানো লাঠি, তার মাথায় একটি নুড়ি বসানো, নিজেই শখ করে লাগিয়ে রেখেছিলেন। ছেলেবেলায় নুড়িটি টেনে খুলতে যেতুম, তিনি বলতেন, ‘খুলো না, ভাই, খুলো না। লাঠির ভিতরে একটি ময়ূর আছে, ছিপি খুললেই বেরিয়ে যাবে।’ মুর্শিদাবাদের গেঁটে বাঁশের দরোয়ানি লাঠি, নাটকে দরোয়ান সাজতে হত তাঁকে, তখন ওই লাঠি কাজে লাগত। সেই তিনিই বলেছিলেন, ‘জানো, ভাই? এবাড়িতে দাড়ির প্রচলন এই আমা হতেই।’ সেই লাঠিটি দিয়ে দাদার একটি ছবিতে ফ্রেম করেছিলুম।
নবীনবাবুও ছিলেন বড় মজার লোক। বাজি রেখে চলন্ত মেল-ট্রেন থামিয়ে চাকরি খোয়ালেন। বাতে পঙ্গু হয়ে শুয়ে আছেন; চোর ঘরে ঢুকে সব জিনিসপত্তর নিয়ে গেল চোখের সামনে দিয়ে, নড়বার শক্তি নেই, চেঁচিয়েই সারা। স্ত্রীর সঙ্গে একটু ঝগড়াঝাঁটি হ’লেই চাকর প্রেমলালকে ডাকতেন, ‘আমার ছুরিটা নিয়ে এসো, গলায় দেব। এ প্রাণ আর রাখব না।’ চাকর বেশ শানানো ছুরি এনে হাজির করলে বলতেন, ‘ওটা কেন? আমার সেই আম-কাটা ভোঁতা ছুরি নিয়ে এসো।’ এমন কত মজার মজার ঘটনা সব। তিনিও একদিন চলে গেলেন।
মার বড় নাতি, দাদার বড় ছেলে গুপুর বিয়ে হল। দক্ষিণের বারান্দা ঝাড়ে লণ্ঠনে আটচালায় মতিবাবু একেবারে গন্ধৰ্বনগর করে সাজিয়ে দিলেন। নাচে গানে থিয়েটারে জমজমাট হয়ে উঠল বারমহল, অন্দরমহল, নাচঘর, বাগান, দক্ষিণের বারান্দা, সারা জোড়াসাঁকোর বাড়িটাই।
তারপর কলকাতার প্লেগ এল, ভূমিকম্প এল। তেতলা বাড়ি ছেড়ে গেলুম চৌরঙ্গীতে। সেইখানে গুপু মেনিন্জাইটিস্ রোগে চলে গেল আমার মায়ের কোলে মাথা রেখে। মা তার ছোট্ট বউকে বুকে নিয়ে কেঁদেছিলেন, ‘আমার সব পুরোনো শোক আজ আবার নতুন করে বুকে বাজল রে।’ ফিরে এলুম আবার সেই দক্ষিণের বারান্দাওয়ালা জোড়াসাঁকোর পারের বাড়িতে।
মস্ত ঝড়খাওয়া জাহাজ যাত্রী নিয়ে ফিরে এসে লাগলো বন্দরে। মার মন খারাপ। কি করে তাঁদের মন শান্ত হয় সকলেরই এই ভাবনা। মা আবার ভাবছেন, আমরা কি করে সান্ত্বনা পাই। দিন যায় এইভাবে। দীনেশবাবু এলেন সে সময়ে, তিনি একদিন এনে উপস্থিত করলেন ক্ষেত্রনাথ চূড়ামণিকে। ঠিক হল রীতিমত ভাগবত কথা শুনব। মাকে বলে বন্দোবস্ত করা গেল। কথকের বেদী পাতা গেল নাচঘরে। কথকঠাকুর বেদী জমিয়ে বসলেন। ছেলে বুড়ো, চাকর দাসী, কর্মচারী, আত্মীয় বন্ধু সবার কাছে খবর রটে গেল—কথকতা হবে। চললো কথকতা মাসের পর মাস। খুব জমিয়ে তুললেন ক্ষেত্রনাথ কথক। যেন তিলেভাণ্ডেশ্বর মহাদেবটি, নধর কালো দেহ। চিকের আড়ালে মা বসে শোনেন গুপুর বিধবা বউকে কোলের কাছে নিয়ে। ক্ষেত্রনাথ কথকের বলার ধরন চমৎকার, গলাও ছিল সুমিষ্ট। দক্ষিণের বারান্দার গায়ে নাচঘরটা তখন অস্তমিতমহিমা গন্ধৰ্বনগরের মত ম্লান শোভা ধারণ করেছে। তারই মধ্যে ক্ষেত্রনাথ কথক মায়ের মনের অবস্থানু্যায়ী এক-একটি কথা ভাগবত থেকে বলে চলেছেন, এই ভাবে গেল প্রায় এক বছর।
তার পর রবিকা একদিন পরগণা থেকে ফিরে এসে বললেন, ‘শিবুৰ্কীর্তনীয়াকে এনে গান শোনাও। ছোটবউঠানের ভালো লাগবে, তোমাদেরও ভালো লাগবে, ওরকম আমি আর শুনিনি।’ রবিকা ডেকে পাঠালেন তাকে, এল শিবুকীর্তনীয়া। সে যা জমালে। কীর্তনীয়া ছিল বটে, কিন্তু সে ছিল সত্যিই আর্টিস্ট। তার ছবি আছে, দাদা এঁকেছিলেন। মোটাসোটা চেহারা, ভাবছি এই চেহারায় কেমন করে সে রাখালবালকদের গোষ্ঠলীলা গাইবে। কিন্তু সে যখন ‘ওহে ওহে’ বলে সুর আরম্ভ ক’রে, ‘আবা আবা’ বলে রাখালবালক হয়ে গান ধরলে, তখন অবাক্। অনেকদিন চলেছিল গান, মাথুর থেকে আরম্ভ করে সমস্ত কৃষ্ণলীলা শুনিয়েছিল সে।
সেই সময় ক্ষেত্রনাথ কথকের ছুটি হয়ে গেল। তিনি বলে গেলেন, ‘রবিবাবু এসে আমার জমাট আসরটা ভেঙে দিলেন।’ আমার কাছ থেকে একটি ছবি তিনি নিয়েছিলেন চেয়ে। তাঁরই বর্ণনামত এঁকেছি পদ্মফুলের উপরে দাঁড়িয়ে বালক কৃষ্ণ। তিনি বলেছিলেন পুজো করবেন। তাঁর সঙ্গে সেই ছবি কাশীতে গেল। তার পর তিনি মারা যাবার পর সে ছবি হাত ফিরতে ফিরতে কোথায় গেল জানিনে। সেদিন দেখি কোন্ এক কাগজে তা ছাপিয়েছে।
তার পর একদিন মাও গেলেন। দাদাও গেলেন জোড়াসাঁকোর বাড়ি শূন্য করে।
ক্ৰমে ক্রমে আমার দক্ষিণ বারান্দার জলসা বন্ধ হল। লক্ষ্ণৌতে গিয়েছিলুম রবিকার সঙ্গে। গোমতীর উপরে বাদশার আমদরবারের ভগ্ন স্তূপে বসে মনে পড়ত আমার দক্ষিণের বারান্দার আড্ডা। তার পর যখন সত্যিই সেই দক্ষিণের বারান্দা প্রায় ভগ্নস্তুপে পরিণত হয়েছে তখনো মায়া ছাড়তে পারিনি। ভাই বন্ধু সঙ্গী ছাত্র সব চলে গেছে; অতবড় খালি বাড়ির সেই দক্ষিণ বারান্দায় একা বসে আমি পুতুল গড়ি, বৈচিত্র্যহীন জীবনে ওইটুকু বৈচিত্র্য আছে তখনো।
এমন সময়ে একদিন ফেলাবতী এসে হাজির। কোথা থেকে উঠে এলো এতটুকুন মেয়েটি, নেড়া ভোলা চেহারা; বললুম, ‘কে তুই?’
‘আমি ফেলা।’
‘ও, ফেলা, তা এসো।’
দেখে বড় আনন্দ হল। যখন ফেলে-দেওয়া জিনিস নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছি, নতুন রূপ দিচ্ছি, তখন এল ফেলাবতী আমার। বললুম, ‘কোত্থেকে আসিস? ঘর কোথায়?’
বললে, ‘এই এখান থেকেই।’ বলে রাস্তার মোড়ের দিকটা দেখালে।
‘কে আছে তোর?’
‘মা আছে।’
‘কি নাম?’
‘কৌমুদী।’
‘বাপের নাম কি?’
‘বসন্ত।’
ভাবছি, এ কোন্ ফেলা এল। মনে হল না, সে মানুষ।
বললুম, ‘কি চাই তোর?’
‘আমি এখানে বসে খেলা করিনে একটু?’
‘তা বেশ তো, কর্ তুই খেলা। বলি, ফেলা একটা সন্দেশ খাবি?’
‘তা খাব।’
রাধুকে বলি, ‘রাধু, আমার ফেলার জন্যে সন্দেশ নিয়ে আয় একটা।’ সে মুখ বাঁকিয়ে চলে যায়। একটা সন্দেশ আর মাটির গেলাসে জল এনে দেয়। ফেল সন্দেশ খেয়ে জল খেয়ে গেলাসটি এক কোণায় রেখে দেয়।
বলি, ‘কেমন লাগল?’
ফেলা বলে, ‘তোমাদের সন্দেশ কেমন আঠা-আঠা, গলায় লেগে যায়। মা খাওয়ায় কটকটে সন্দেশ, সে আরো ভালো।’
‘তা বেশ।’ এমনি রোজ আসে সে সন্দেশ খাইয়ে ভাবসাব করি। সে একপাশে বসে খেলে, আমিও খেলি। ভাঙা কাঠকুটো নুড়ি দিই। সে বসে তাই দিয়ে খেলা করে। পাশের একটা টেবিলে পুতুল গড়ে গড়ে রাখি।
সে বললে, ‘এগুলোর ধুলো ঝেড়ে রাখি?’
‘তা রাখো।’
সে ধুলো ঝাড়ে, তাতে হাত বোলায়।
‘বলি, পুতুল নিবি একটা?’
‘না, পুতুল দিয়ে কি করব? আমায় নুড়িগুলো বরং দাও।’
‘কি করবি তুই?’
‘ভাইকে দেব, ঘুঁটি খেলাবে।’
কোনোদিন চায় পুরোনো খবরের কাগজ, বাপকে দেবে, বাপ ঠোঙা করে বাজারে বেচবে। কোনোদিন বা চায় পুরোনো টিনের কৌটা, মাকে দেবে, মা মসলাপাতি রাখবে।
এমনি রোজই আসে। হঠাৎ আসে নিঃশব্দে, বুঝতে পারিনে কোথা দিয়ে আসে। বিনিপয়সার খেলুড়ি ফেলা নিঃসঙ্গ দিনের, মানুষের মধ্যেও সে ফেলা, কাঠকুটরো, ছেঁড়া টুকরো কাগজেরই সামিল। যত ফেলা জিনিস কুড়িয়ে বাড়িয়ে এক বুড়ো আর এক মেয়ে খেলা জুড়েছি সেই দক্ষিণের বারান্দায়। একদিন ফেলা বললে, ‘তোমাদের বাড়ির ভিতরটা দেখাবে আমায়?’
‘দেখবি?’
রাধুকে ডেকে বললুল, ‘নিয়ে যা একে বউমার কাছে, বাড়ির ভিতর দেখতে চায়।’
বউমা আবার তাকে একপেট খাইয়ে দিলে। সে পাকা গিন্নির মত সব ঘুরে ঘুরে দেখে ফিরে এল।
বললুম, ‘দেখা হল, ফেলাবতী, বাড়ির ভিতর?
বললে, ‘হ্যা।’
‘তবে এবার তুই বাড়ি যা, আমিও উঠি, নাইতে খেতে হবে।’
দক্ষিণের বারান্দায় সেই শেষ প্রবেশ ফেলাবতী ও আমার। তার পর অসুখে পড়লুম। সেই অবস্থাতেই শুনি দক্ষিণের বারান্দা বিকিয়ে গেছে মাড়োয়ারিদের হাতে। রোগী আমি, একটা মাস মেয়াদ পেয়েছি আর এবাড়িতে থাকবার।
০৯. মধুর শেষ নেই
মধুর তোমার শেষ যে না পাই,
প্রহর হল শেষ।
এ ‘মধুর শেষ নেই। প্রহর শেষ হয়ে যায়। কত মধুর, আমাদের এমন পাত্র তাতে এর এক ফোঁটা মধুও ধরতে পারিনে। ধুলোতেও মধু, তাই তো বলি, গোরুর গাড়ি রাস্তার বুক চিরে চলেছে আঁকলেম, কিন্তু ধুলো উড়ল কই?’ ধুলো উড়োনো চাই। সেবারে এখানেই এই চেয়ারে এমনিভাবেই বসে বাস দেখতুম, রাস্তার পরে ওই গাছটির উপর দিয়ে লাল ধুলো উড়ে এল, দেখতে দেখতে গাছটি ঢেকে গেল, আবার ধীরে ধীরে গাছটি পরিষ্কার হয়ে ফুটে বের হল, ধুলোর হাওয়া চলে গেল আরো এগিয়ে, মনে হল গাছটির উপরে যেন একপশলা লাল ধুলোর বৃষ্টি হয়ে গেল। সে কি চমৎকার। তা কি আঁকতে পারি? পারিনে। কিন্তু আঁকতে হবে যদি সময় থাকে, এই বৃদ্ধকালেও দেখো মন সঞ্চয় করে রাখছে, কোন্ জন্মের জন্য বলতে পারো?
একবার কি হল, আমার চোখের চশমার একটা কাঁচের কোণা ভেঙে গেল। তাই চোখে দিয়ে থাকি। বললুম, আরো ভালোই হয়েছে শার্শি ফাঁক হয়ে গেছে, ওর ভিতর দিয়ে রং আসবে। একদিন নন্দলালকে বললুম, দেখো তো আমার এই চশমাটি চোখে দিয়ে। নন্দলাল তা চোখে দিয়ে বললে, এ যে রামধনুকের রং দেখা যায়; অনেকদিন বুঝি পরিষ্কার করেননি কাঁচ। আমি বললুম, না ন, তা নয়। ছবিতে যত রঙ দিই সেই রঙই এই রাস্তায় লেগেছে।
আমার হৃদয় তোমার আপন হাতে দোলে দোলাও
দোলাও দোলাও।
মায়ের দোল স্মরণ হয়। যাবার সময় তো হইছে, যাবই তো, এ ঘাটের ধাপ শেষ হয়ে এসেছে। নদীর ওপরে গিয়ে কি দেখব? আবার কি মিলব সবাই সেখানে? কি জানি। তা যদি জানতে পারা যেত তবে কিন্তু পৃথিবীতে বেঁচে থাকার রস চলে যেত। এইখানেই সব শেষ করে নাও; এখানকার পাত্র এইখানেই ধুয়ে ফেলো। শেষ পেয়ালার ফোঁটা ফোঁটা তলানিটুকু, সেখানেই সব রস জমা হয়ে আছে। যত শেষের দিকে যাবে তত রস। চীনেরা বেশ উপমা দেয় তাদের চায়ের সঙ্গে, বলে, চা তিন রকম। প্রথম জ্বালের চা ঢাললে, ছোট ছেলেরা খাবে, পাতলা চা, সোনার বর্ণ, তাতে একটু দুধ একটু চিনি। দ্বিতীয় জ্বাল, তখনো সেটা ফুটছে রং আগের চেয়ে একটু ঘন হয়ে এসেছে, তা প্রৌঢ়দের জন্য। আর তৃতীয় জ্বাল, তলায় যে চা রয়েছে অল্প জল আর চায়ের ক্বাথ, এই যে শেষ পেয়ালা, এ সবার জন্য নয়। যাদের বয়েস হয়েছে, সুখ-দুঃখ তিক্ত মিষ্টের রস সত্যি উপভোগ করতে পারে এ শুধু তাদের জন্যই।
কালি কলম মন
লেখে তিনজন।
ছবিটি আঁকি তুলিটি জলে ডোবাই, রঙে ডোবাই, মনে ডোবাই, তবে লিখি ছবিটি। সেই ছবিই হয় মাস্টারপিস। অবিশ্যি, সব ছবি আঁকতে যে এভাবে চলি তা নয়। জলে ডুবিয়ে রঙে ডুবিয়ে অনেক ছবির কাজ সেরে দিই, মন পড়ে থাকল বাদ । এমন ছবি একটা একে যদি ছিঁড়ে ফেলতে যাই, তোমরা খপ করে হাত থেকে তা ছিনিয়ে নিয়ে পালাও। ঠকে যাও জেনো।
আমি যৌবনে দেশী সংগীতের স্বর ধরতে চেয়েছিলেম, হাতের আঙুলের ডগায় সুর এসেওছিল; কিন্তু মনে তো পৌঁছয়নি। ব্যর্থ হয়ে গেল আমার সকল পরিশ্রম, সকল সংগীতচর্চা, এক-একবার এই মনে করি। কিন্তু চিত্রকর হয়ে চিত্রকর্মে যেদিন প্রথম শিক্ষা শুরু করলেম সেইকালের একটা ঘটনা বুঝিয়ে দিয়েছিল মন আমার সুর সংগ্রহ করতে একেবারেই উদাসীন ছিল না।
তখন কলকাতায় ওয়েল্স্লি পার্কের কাছে মাদ্রাসা কলেজ, সামনে একটা দিঘি, তার পারে ইটালিয়ান আর্টিস্ট গিলার্ডি সাহেবের বাসা। তাঁর কাছে রোজ সকালে যাই, দস্তুরমত দক্ষিণা দিয়ে প্যাস্টেল ড্রইং আর অয়েলপেন্টিং শিখি। বেশ ঘরের লোকের মতই আমার সঙ্গে ব্যবহার করেন সাহেব। স্টুডিয়োর একদিকে আমি বসে ছবি আঁকি; অন্যদিকে তাঁর মেম ছেলেকে দুধ খাওয়াচ্ছেন; দু-একটি আবার স্কুলে যায়, তাদের খাইয়ে দাইয়ে তৈরি করে স্কুলে পাঠাচ্ছেন; কখনো বা আমার গাড়িতে করে বাজারটা ঘুরে আসছেন। সে বাড়ির নিচের তলায় থাকে মান্ধাটা নামে এক বুড়ো ইটালিয়ান মিউজিক মাস্টার আর তার মেয়ে। বুড়ো বাপেতে মেয়েতে থাকে বেশ, রোজ সকালে মেয়ে পিয়ানো বাজায় বাপ বাজায় বেহালা। সুর আসে ভেসে, উপরে বসে আমি সেই বিলিতী সুর শুনি আর ছবি আঁকি। একদিন সকালে রোজকার মত ছবি আঁকছি, নিচে থেকে বেহালার সুর এল কানে, উদাস করে দিলে। হাত বন্ধ করলুম তুলি টানার কাজ থেকে, সুর তো নয় যেন বেহালাটা কাঁদছে। সেদিন সে সুর স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে, বেহালার ছড়ি, বেহালার তার আর যে বাজাচ্ছে তারও মানসতন্ত্র এক হয়ে গেছে। আজ আর পিয়ানো নেই সঙ্গে। গিলার্ডিকে বললুম, ‘সাহেব আজ বেহালা যেন কাদছে মনে হচ্ছে কেন বলো তো? এমন তো শুনিনি কখনো?’ সাহেব বললেন, ‘চুপ চুপ, জানো না বুড়োটির মেয়ে কাল চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে?’ সেদিন আর ছবি আঁকা হল না আমার। খানিক বাদে আস্তে আস্তে নেমে এলুম। সিঁড়ির কাছের ঘরটিতে দেখি, বুড়োটি বসে আছে চেয়ারে, কাঁধে বেহালাটি রেখে মাথা হেঁট করে, একমাথা সাদাচুল পাখার হাওয়ায় উড়ছে বুঝেছিলুম সেদিন, মনে ধরল আজ সুরের আগুন। অন্তর বাজে তো যন্তর বাজে। মনের স্পর্শ নইলে গাওয়াও বৃথা, বাজানো বৃথা, ছবি আঁকাও বৃথা, এ কথা জেনে নিলে মন।
ছেলেছোকরারা আঁকে দেখবে—দেয়ালি পট, ঝাড়লণ্ঠন, একটু রঙ রেখা, ভুলে গেল তাতেই। তার পর এল রসের প্রৌঢ়তা, যেমন মোগল আমলের আর্টের মধ্যে দেখি; তাদের রঙ, সাজসজ্জা, সে কি বাহার। তার পর সেই বাহার থেকে পৌঁছল গিয়ে রসের আরো উচু ধাপে আর্ট, তবে এল বাইরের-রঙচঙ-ছুট ছবি সমস্ত, যেন মেঘলা দিনের ছায়া, স্নিগ্ধ, গম্ভীর। আর্টের এই কয়টি সোপান মাড়াতে হবে, তবে হয়তো আর্টিস্ট বলতে পারব নিজেকে।
একবার কেষ্টনগরের এক পুতুলগড়া কারিগর জ্যোতিকার একটা মূর্তি গড়লে। অমন তো সুন্দর চেহারা তাঁর, যেমন রঙ তেমনি মুখের ডৌল—মূর্তি গড়ে তাতে নানা রঙ দিয়ে এনে যখন সামনে ধরলে সে যা বিশ্ৰী কাণ্ড হল, শিশুমনও তা পছন্দ করবে না। মাটির কেষ্টঠাকুরের পুতুল বরং বেশি ভালো তার চেয়ে। পুতুল গড়া সোজা ব্যাপার নয়। তার গায়ে এখানে ওখানে বুঝে একটু আধটু রঙ দেওয়া, চোখের লাইন টানা, একটু ফোঁটা দিয়ে গয়না বোঝানো, এ বড় কঠিন। সত্যি বলব, আমি তো পুতুল নিয়ে এত নাড়াচাড়া করলুম, এখনো সেই জিনিসটি ধরতে পারিনি। একটু ‘টাচ’ দিয়ে দেয় এখানে ওখানে, বড় শক্ত তা ধরা। সেবার পরগণায় যাচ্ছি বোটে, সঙ্গে মনীষী আছে। কোথায় রইল সে এখন এক-একা পড়ে, কি শিখল না-শিখল একবার লড়তে এলে তো বুঝব। তা সেবারে খাল বেয়ে যেতে যেতে দেখি এক নৌকোবোঝাই পুতুল নিয়ে চলেছে এক কারিগর। বললুম, ‘থামা, থামা বোট, ডাক্ ওই পুতুলের নৌকো।’ মাঝিরা বোট থামিয়ে ডাকলে নৌকোর মাঝিকে, নৌকো এসে লাগল আমার বোটের পাশে। নানা রঙবেরঙের খেলনা তার মাঝে দেখি কতকগুলি নীল রঙের মাটির বেড়াল। বড় ভালো লাগল। নীল রঙটা ছাই রঙের জায়গায় ব্যবহার করেছে তারা, ছাই রঙ পায়নি নীলেই কাজ সেরেছে। অনেকগুলো সেই নীল বেড়াল কিনে ছেলেমেয়েদের বিতরণ করলুম। পুতুলের গায়ের ‘টাচ’ বড় চমৎকার। পটও তাই, এই জন্যই আমার পট ভালো লাগে, বড় পাক৷ হাতের লাইন সব তাতে।
হ্যাঁ, মনীষীর লড়াইয়ের কথা বলছিলুম। সেই লড়াইয়ের এক সুন্দর গল্প মনে এল। অনেক কাল আগের কথা। একজন লোক, তাঁর পূর্বপুরুষ ভালো মৃদঙ্গ-বাজিয়ে, নিজেও বাজায় ভালো। সে বলেছিল, মৃদঙ্গ বাজিয়ে আমার সুখ হল না। গণেশ আসত, তার সঙ্গে একহাত পাল্লা দিয়ে বাজাতে পারতুম তবে সুখ হত। গণেশের কাছে হার হলেও তার সুখ, সে শুধু সমানে সমানে পাল্লা দিতে চেয়েছিল। কিছুকাল বাদে তার নাতি এল। বলে, ‘খেতে পাচ্ছিনে।’ বললুম, ‘কেন, এতবড় বাজিয়ের নাতি তুমি, খেতে পাচ্ছ না, সে কি কথা। আচ্ছা, কত হলে তুমি থাকবে আমার কাছে?’ অল্পসল্পই চাইলে। রাখলুম তাকে আমার বাড়িতেই। তখন আমার ভয়ানক বাজনার শখ, এসরাজ বাজাই। শ্যামসুন্দরও আছে। ছেলেটি বললে, ‘আমায় কি করতে হবে?’ বললুম, ‘কিছুই না। সন্ধ্যেবেলা তুমি মৃদঙ্গ বাজাবে, আমি শুনব।’ প্রথমদিন সন্ধ্যেবেলা বারান্দায় যেমন বসি এই রকম দেয়ালের কাছে চৌকি টেনে বসেছি, সে মৃদঙ্গ বাজাবে। বললে, ‘গান চাই।’ শ্যামসুন্দরকে বললুম, সে আস্তে আস্তে গান ধরলে, আর ছেলেটি বাজালে। কি বাজাল, যেন মেঘের গুরু গুরু শুনতে থাকলেম। মৃদঙ্গ বাজছে, সত্যি যেন আকাশে দুন্দুভি বাজছে। রবিকা লিখে গেছেন, বাদল মেঘে মাদল বাজে। ঠিক তাই, এ বাদ্যযন্ত্র বাজছে, না মেঘ। সেদিন বুঝলুম, তার ঠাকুরদা যে বলেছিল গণেশের সঙ্গে পাল্লা দেবে, তা কেন বলেছিল। রবিকাও আসতেন কোনো-কোনোদিন, বসে মৃদঙ্গ শুনতেন সন্ধ্যেবেলা। শুনে খুব খুশি। বলতেন, ‘অবন, একে হাতছাড়া কোরো না তুমি।’ তাকে সমাজে কাজ দেবার কথা হয়েছিল। কিন্তু সমাজের কর্তারা বললেন, আর-একজন বাজিয়ে আছে এখানে, তাকে সরিয়ে কি করে একে নিই, ইত্যাদি। এই করতে করতে কিছুদিন বাদে দ্বারভাঙ্গার রাজার নজরে পড়ল। বেশি মাইনে দিয়ে আমার কাছ থেকে তাকে লোপাট করে নিয়ে গেল। রবিকা কোথায় গিয়েছিলেন, ফিরে এসে বললেন, ‘অবন, তোমার সেই বাজিয়ে?’ বললুম, ‘চলে গেল রবিকা।’ গুণীর গুণ কি চাপা থাকে? আগুনকে তো চেপে রাখা যায় না। সেই এক শুনেছিলুম মৃদঙ্গ বাজনা। অনেক খোলওয়ালাকে থামাতে হয় গানের সময়ে। এত জোরে তাল বাজায় যে সে-শব্দে গান চাপ পড়ে যায়, ইচ্ছে হয় ছুটে গিয়ে তার হাত চেপে ধরি।
এই দেখো, বাজনার কথায় আর-একটা মজার কথা মনে পড়ে গেল। এক বীনকার, নামধাম বলব না, চিনে ফেলবে, বড় ওস্তাদ, খুব নামডাক হয়েছে; লক্ষ্ণৌর নবাব তখন মুচিখোলায় বন্দী হয়ে আছেন, এবারে যাবে তাঁকে বাজনা শোনাতে। নিজে খুব সেজেছেন, চোগাচাপকান পরেছেন, জরির গোল টুপি মাথায়, নিজের নামের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন মস্ত একটা হিন্দুস্থানী উপাধি, অমুকজি বীনকার, বীণাটাকেও জড়িয়েছেন নানা রঙের মখমলের গেলাপে। ইচ্ছে, নবাবকে বীণা শুনিয়ে মুগ্ধ করে বেশ কিছু আদায় করবেন। একদিন সকালে বীণা নিয়ে উপস্থিত মুচিখানায়। খবর গেল, ‘কলকাত্তাসে এক বড় বীনকার আয়া—হুজুরকে দরবারমে।’ খবর পাঠিয়ে বসে আছেন দেওয়ানখানায়। নবাব উঠবেন, হাতমুখ ধোবেন, সে কি কম ব্যাপার? নবাব উঠে হাতমুখ ধুয়ে তৈরি হয়ে পান চিবোতে চিবোতে সটকা মুখে মজলিশে এসে বসে হুকুম করলেন, ‘তেরা বীনকারকো বোলাও।’ নবাবের এত্তালা পেয়ে বীনকার উপরে উঠে নবাবকে সেলাম ঠুকে সামনে কায়দা করে বসে বীণার গেলাপ খুলতে লাগলেন এক-এক করে। এখন, নবাবদের কাছে যার বাজাতে যায় তারা আগে থেকে বীণার তার বেঁধে যায়, গিয়েই বাজনা আরম্ভ করে দেয়। আর বীনকার ওখানে বসেই অনেকক্ষণ ধরে তার বেঁধে সুর ঠিক করে, বীণাটি হাতে নিয়ে যেই না দু বার প্রিং প্রিং করেছেন, নবাব বলে উঠলেন, ‘ব্যস্ করো।’ নবাবী মেজাজ, তাদের ‘ব্যস্’ বলা কি বোঝ তো? বীনকার তক্ষুনি বীণা গুটিয়ে সরতে নবাব বললেন, ‘দেওয়ান, ইস্কো শ’ও রূপেয়া ইনাম দেও। আউর বোলো দোসরা দফে মুচিখানেমে আনেসে উসকো বীন ছিনা জায়েগা।’ নবাব ছেড়ে দাও, আমি নিজেও যে নবাবি করেছি এককালে, নাচ গান বাজনা বাদ রাখিনি কিছু। বলেছি তো সে সব তোমায়। কিন্তু ওদিকটা হল না আমার, তা কি করব। ভিতরে সুর নেই যন্তর বাজিয়ে করব কি? কিন্তু কার হাতে কেমন সুরের পাখি ধরা দেয় কে বলতে পারে।
একটি ছোকরা আসত তখন আমার কাছে। সারেঙ্গি বাজাত। প্রফুল্ল ঠাকুরের ছেলের বিয়ে, মহা ধুমধাম বিরাট ব্যাপার, গিয়েছি সেখানে। শুনছি কে এক বাজিয়ে সুরবাহার বাজাবে। খুব বলাবলি হচ্ছে। ভাবছি কে এমন ওস্তাদ বীনকার। সভায় বসেছি, এবারে বাজনা শুরু হবে। দেখি, সেই ছোকরাটি একটি বীণা হাতে এল বাজাতে। চিনতেই পারা যায় না তাকে আর। বললুম, ‘তুমিই বীণা বাজাবে?’ সে বললে, ‘হাঁ হুজুর, একটু একটু শিখেছি।’ বললুম, ‘বেশ, বেশ, বাজাও শুনি।’ মনে পড়ে এতটুকু ছোকরা সারেঙ্গি বাজাত, হঠাৎ দেখি সে এক মস্ত ওস্তাদ, সভায় বাজনা শোনায়। হয়, যে এক কালে কিছুই জানত না, সে একদিন বীণাও বাজাতে পারে। কতই দেখলেম।
আরো শোনে। একবার বাংলা থিয়েটারে গেছি, বুড়ো অমৃত বোস, বড়ো ভালো লোক ছিলেন, পাশে বসে আছেন। আর, মিনার্ভা থিয়েটারে ভালো সিন আঁকত, স্টেজ ডেকোরেশন করত, নামটা তার মনে পড়ছে না, আমিই তাকে রেকমেণ্ড করে দিয়েছিলুম, সেও আছে একপাশে বসে। কি একটা অভিনয় হল। অমৃত বোসকে বললুম, ‘দেখুন মশায়, আপনাদের অ্যাক্টর অ্যাকট্রেসরা সিংহাসনে বসবে, বসতেই জানে না, গড়গড়ার নলে টান দিতে পারে না। একটা স্টুডিয়ো করুন, যেখানে তারা এইসব শিখবে। উঠতে বসতে যারা জানে না, তার ‘প্লে’ করবে কি আবার?’ তিনি বললেন, ‘তা বলেছেন ভালো; এটা করতে হবে এবারে।’ অন্য আর-এক রাত্তিরে স্টার থিয়েটারে কি এক সিনে আর-এক আর্টিস্ট রাজসভার সিন এঁকে পিছনে ঝুলিয়ে দিয়েছে, বৃহৎ সভা, ঘরের থাম আসবাবপত্র কিছুই বাদ রাখেনি আঁকতে। এখন সেই সিনে রাজার সিংহাসন পড়েছে। রাজা বসলেন এসে সিনের পার্সপেক্টিভে যেখানে পাপোশটি রাখা আছে ঠিক সেইখানে একটা চৌকিতে। অতিরিক্ত পার্সপেক্টিভের ফল দেখো ছবিতে। রাজার স্থান হল পাপোশের জায়গায়।
আর একবার এই রকম পার্সপেক্টিভের ধাঁধাঁয় পড়েছিলেম ছাত্রদের নিয়ে। নন্দলালরা তখন ছাত্র। আর্টস্কুলে আমি কাজ করি। রাশিয়া থেকে একটি মেম এল। বললে, ‘বুদ্ধের ছবি আঁকব, ঘর চাই একটা।’ ছবি আঁকবে ঘর চাই, তার কি করি। আর্টস্কুলে এখন তোমার দাদার যেটা ড্রইং রুম সেই ঘরটা ছেড়ে দিলুম। সে ঘরের চাবি চেয়ে নিল, বললে, একলা ঘরের দরজা বন্ধ করে নিশ্চিন্তমনে ছবি আঁকবে। আচ্ছা তাই হোক। মেমটি রোজ আসে, ছবি আঁকে, আমি মাঝে মাঝে যাই। উত্তরদিকের দেয়াল জুড়ে কাগজ সেঁটেছে। কাজের সময় ছাড়া বাদবাকি সময় পরদা টেনে ছবি ঢেকে রাখে। ছাত্রেরা কেউ যেতে পারে না কি হচ্ছে দেখতে। নন্দলাল বললে, ‘কী করে ড্রইং করে দেখতে চাই।’ মেমকে বললুম সে কথা, ‘আমার ছাত্রদের দেখাও একবার, কি করে তুমি ড্রইং কর। সে বললে, ‘আর কয়েকদিন বাদে আমার পেনসিল ড্রইং শেষ হয়ে যাবে, তখন দেখাব।’ কদিন বাদে খবর দিলে, ‘এবারে আসতে পারো।’ নন্দলালদের নিয়ে গেলুম। ছবির পরদা সরিয়ে দিলে। প্রকাণ্ড কাগজে বুদ্ধের সভা আঁকছে—ও মা, পার্সপেক্টিভ এমন করেছে, নিচে থেকে উপরে উঠে সেই কোথায় বুদ্ধদেব বসে আছেন নজরে পড়ে না। এ কি ছবি, এ কি পার্সপেক্টিভ? মেম বললে, ‘কারেক্ট্ পার্সপেক্টিভ হয়েছে।’ নন্দলাল বললে, ‘পার্সপেক্টিভের চূড়ন্ত হয়েছে, কিন্তু চিত্রের কিছু নেই এতে।’ পরে শুনি সেই ছবিই কোন্ এক রাজার কাছে বিক্রি করে অনেক টাকা হাতিয়ে চলে গেছে সে দেশে।
কত সুখদুঃখের মান-অপমানের ধাক্কা খেয়ে খেয়ে আর্টিস্টের মন তৈরি হয়। আমরা সব সৃষ্টিছাড়া; প্রকৃতি মায়ের আদুরে, কোলের কাছাকাছি ছেলে; একটা বুনো ভাব আছে। সবার সঙ্গে মেলে না, সত্যিই তাই। সুখদুঃখ আমাদের বেশি করে বাজে, জীবন উপভোগ করবার ক্ষমতাও আমাদের বেশি। প্রকৃতি আমাদের বেশি করে দিয়েছে সবই। একটু আলো দেখি, ছুটে বেরিয়ে পড়ি। সেটিমেণ্টাল?—ঠিক তা নয়। অবিশ্যি এ কথা বলে অনেকেই আমাদের বেলায়। সেবারে কি হয়েছিল—এই ভাবুকতার জন্য কেমন তাড়া খেয়েছিল দুটো ছেলে। রবিকা বেঁচে, এসেছি এখানে। ভোরবেলা সূর্য ওঠবার আগেই খোয়াইর দিকে ছুটতুম। একদিন ছুটছি, ছুটছি, তালগাছ পেরিয়ে গেলুম, খেজুরগাছ দুটোও পেরিয়ে গেলুম, শরগাছের ঝোপগুলির কাছাকাছি এসেছি—দুটো ছেলে, তারাও বুঝি বেড়াতে বেরিয়েছে, বললে, ‘ফিরে দেখুন কি সুন্দর সূর্য উঠেছে।’ আমি তখন হন হন করে হাঁটছি। দিলুম এক তাড়া মেরে, ‘যাঃ যাঃ, কী সুন্দর সূর্য উঠেছে, তোরা দেখ্গে, আমি বলে হেঁটে হয়রান।’ ফিরে এলুম; দেখি রবিকা বসে আছেন চা আগলে নিয়ে। তাড়াতাড়ি এসে বসলুম টেবিলে। রবিকা বললেন, ‘কোথায় গিয়েছিলে তুমি। এদিকে আমি চা নিয়ে বসে আছি তোমার জন্যে। নাও, খাও।’ বলে এটা এগিয়ে দেন, ওটা এগিয়ে দেন। রবিকার সামনে বসে খাওয়া, সে কি ব্যাপার জানোই তো। তার পর চায়ের সঙ্গে আমার একটু রুটি চলে শুধু। রবিকা বললেন, ‘একটু গুড় খাও দেখিনি। গুড়টা ভালো জিনিস।’ সকালবেলা গুড়! মহামুশকিল, এদিক ওদিক তাকাই; রবিকা আবার মস্ত একটি কেক এগিয়ে দিলেন, ‘খাও ভালো করে।’ একটা ছুরি দিয়ে একটুকরো কেক কেটে নিয়ে বাকিটা আস্তে আস্তে ঠেলে দিলুম অ্যাণ্ড্রুজের দিকে। অ্যাণ্ড্রুজ দেখি সবটাই শেষ করে দিলেন। বেশ খেতে পারতেন। যাক, সকলের ফাঁড়া তে কাটল। প্রতিমাকে বললুম, ‘প্রতিমা, যে কয়দিন আছি ভোরের চা-টা তোর কাছেই খাইয়ে দিস। কেন আর বারে বারে আমায় সিংহের মুখে ফেলা।’ তার পরদিন থেকে সকালে উঠে তাড়াতাড়ি প্রতিমার কাছে চা খেয়েই বেড়াতে বের হতুম। ফিরে আসতেই রবিকা বলতেন, ‘অবন, চা খেলে না তুমি?’ মাথা চুলকে বলতুম, ‘প্রতিমা খাইয়ে দিয়েছে।’ মুচকে হেসে তিনি বলতেন, ‘ও বুঝেছি।’
তখন ছেলেরা ওই রকম সেন্টিমেণ্টাল ছিল—ওঃ কী চমৎকার সূর্যোদয় এখানে, আহা হা। যেন আর কোথাও নেই এমন জিনিস। এরই আর একটা গল্প শোনো। সেই বারেই কারপ্লেজও আছে এখানে। বিকেলে এই রাস্তার উপরেই টেবিল পড়ে। সবাই বসে চা খাই। চা গেয়ে কারপ্লেজ ও আমি ঘুরে বেড়াই। একদিন বিকেলে রোজকার মত ঘুরে বেড়াচ্ছি আমরা দুই আর্টিস্টে নানা বিষয় নিয়ে নানা আলাপ করছি। ওদিক থেকে একটি হালকা কুয়াশার চাদর ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে আশ্রমের শালবনের উপর খানিক স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল। ঠিক সন্ধ্যে হচ্ছে সেই সময়টিতে। দু বন্ধুতে এই দৃশ্য দেখে মুগ্ধ। দুজনেই বলে উঠলুম, ‘বাঃ কী চমৎকার।’ মুখে আর কথা নেই কোনো। শুধু বিস্ময়ে বাঃ বাঃ করছি দাঁড়িয়ে। পিছন থেকে রথী-ভায়া বলে উঠলেন, ‘ও কিছুই নয়, মেঘও নয় কুয়াশাও নয়। ও হচ্ছে চাল-কলের ধোঁয়া।’ আরে ছোঃ ছোঃ, রথী ভাই, এ তুমি করলে কি? তুমি আমাদের এত ভাবুকতা এত কবিত্ব এমনি করেই মাটি করে দিলে? কারপ্লেজও বললে, ‘এমনি করে আমাদের স্বপ্ন নষ্ট করে দিতে হয়? জানলেই বা তুমি, আমাদের তা বললে কেন?’ দেখো তো কী কাণ্ড। দু আর্টস্টকে এমনি বেকুব করে দিলে। বেশ ছিলুম তখনকার শান্তিনিকেতনে। ভোরে উঠতুম। রবিকা তো অন্ধকার থাকতেই উঠতেন, সেই ওঁর চিরকালের অভ্যেস। দরজা খোলা, বর্ষাকাল, একটু একটু বৃষ্টি হচ্ছে; হাতমুখ ধুতে ধুতে দেখতুম সেখান থেকে, রবিকার ঘরে উপরে একটি তাকে বাতি জ্বলছে, ঠিক যেন শুকতারাটি জ্বল জ্বল করছে; মনে হত, সমস্ত শাস্তিনিকেতনের উপর যেন আকাশপ্রদীপ জ্বলছে; আর আমরা ছেলেপুলেরা নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি।
পাল্লা দেবার লোক চাই। সেই লোক আর নেই। গণেশকে পেলুম না, কাঠের গণেশ নিয়েই কারবার করে গেলুম। বড়ো খুশি হয়েছিলুম রবিকা যখন ছবি আঁকতে আরম্ভ করলেন। ভাবলুম, এইবারে এক রাস্তায় চলবার লোক পেলুম; এইবার এল বড় ওস্তাদ আমাদের মাঝখানে।
বুড়ো হয়ে গেছি, আর জোর নেই। প্রতিদ্বন্দ্বী এখন না আসাই ভালো। না তা কেন? আসে, তাই তো চাই। ভালোই হবে। কিন্তু দেখছিনে তো কাউকে। এখনো যে অনেক কিছু আছে ভিতরে পড়ে। ভেবেছ নতুন কায়দাতে হার মানব? তা নয়।
এক বুড়ো ওস্তাদের ছাত্র দিগ্বিজয়ী কুস্তিগির হয়ে উঠেছে। দেশবিদেশে তার নাম। সবাইকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়, কেউ পারে না তার কাছেই এগতে। একবার তার শখ গেল গুরুর সঙ্গে কুস্তি করে গুরুকে হারিয়ে নাম কিনতে। রাজা শুনে আয়োজন করবার হুকুম দিলেন। পাড়ায় পাড়ায় ঢোল পিটিয়ে দিলেন দিগ্বিজয়ী কুস্তিগির এবারে গুরুর সঙ্গে কুস্তি লড়বে। দিন ঠিক হল। লোকে লোকারণ্য দুজনের কুস্তি দেখতে। বুড়ো পালোয়ানকে রাজা হুকুম করলেন। সে বলে, ‘হুজুর, বুড়া হো গিয়া, তাকদ নেহি, মর্ জায়েগা। ও ছোকরা হ্যায়।’ কিন্তু রাজার হুকুম, ‘না’ বলবার উপায় নেই। ওদিকে দিগ্বিজয়ী ছাত্র সভায় ঢুকে পাঁয়তারা করছে, ভাবটা বুড়োকে হারাতে আর কতক্ষণ। বুড়ো কি করে! সেলাম ঠুকে লেংটিটা টেনে প’রে মাটি থেকে একটু ধুলো হাতে মেখে সভায় ঢুকল। কুস্তি আরম্ভ হল। প্রথম কয়েক প্যাঁচ বুড়ো হারলে, দিগ্বিজয়ী সাকরেদ সহজেই তাকে ফেলে দেয়। সবাই ভাবলে বুড়ো হারে বুঝি এইবারে। শেষবার সাকরেদ প্যাঁচ দিতে যেমন এসেছে এগিয়ে, বুড়ো এমন এক প্যাঁচ মারলে চোখের নিমেষে সাকরেদ ছিটকে পড়ে গেল অনেকটা দূরে বার কয়েক ডিগবাজি খেয়ে। সভাসুদ্ধ হৈ হৈ। ওস্তাদ সাকরেদের দিকে চেয়ে বললে, ‘হুয়া?’ সাকরেদ উঠে হাত জোড় করে বললে, ‘ওস্তাদজি, এ প্যাঁচ তে আপ শিখলায়া নেহি।’ বুড়ো বললে, ‘নেহি বেটা, আজকে ওয়াস্তে এ প্যাঁচ রাখ্খা থা।’ জানত সাকরেদের শখ হবে একদিন কুস্তি লড়তে; সেইদিনের জন্য ওস্তাদ এই প্যাঁচ রেখে দিয়েছিল।
আমার বেলাও হয়েছিল তাই। ঠিক এই কথাই বলেছিল আমায় আমারই এক নামজাদা ছাত্র। আর্ট সোসাইটিতে আমার সেই পাখির সেটগুলি একজিবিট করেছি, সে দেখে বললে, ‘এ কায়দা তো শেখাননি আমাদের।’ বললুম, ‘সবই শিখিয়ে দেব নাকি?’ অনেক প্যাঁচ এখনো শিখি, রেখে দিই, তোমরা লড়তে এলে তখন শেখাব।
১০. অবন একটা পাগলা
রবিকা বলতেন, ‘অবন একটা পাগলা।’ সে কথা সত্যি। আমিও এক-একসময়ে ভাবি, কি জানি কোন্দিন হয়তো সত্যিই ক্ষেপে যাব। এতদিনে হয়তো পাগলই হয়ে যেতুম, কেবল এই পুতুল আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই নিয়েই কোনোরকমে ভুলে থাকি। নয় তো কি দশাই হত আমার এতদিনে। একটা বয়স আসে যখন এইসব ভুলে থাকবার জিনিসের দরকার হয়। একবার ভেবেছিলুম লেখাটা আবার ধরব, কিন্তু তাতে মাথার দরকার। এখন আর মাথার কাজ করতে ইচ্ছে যায় না। গল্প বলি, এটা হল মনের কাজ। এই মনের কাজ আর হাতের কাজই এখন আমার ভালো লাগে। তাই পুতুল গড়তেও আমার কষ্ট হয় না। সেখানে হাত চোখ আর মন কাজ করে। অন্য আর কিছু ভাবতেও ইচ্ছে করে না। রবিকা যে বৈকুণ্ঠের খাতায় তিনকড়ির মুখ দিয়ে আমাকে বলিয়েছিলেন ‘জন্মে অবধি আমার জন্যেও কেউ ভাবেনি আমিও কারো জন্য ভাবতে শিখিনি’, এই হচ্ছে আমার সত্যিকারের রূপ। রবিকা আমাকে ঠিক ধরেছিলেন। তাই তো তিনকড়ির পার্ট অমন আশ্চর্য রকম মিলে গিয়েছিল আমার চরিত্রের সঙ্গে। ও সব জিনিস অ্যাকটিং করে হয় না। করুক তো আর কেউ তিনকড়ির পার্ট, আমার মত আর হবে না। ওই তিনকড়িই হচ্ছে আমার আসল রূপ। আমি নিজের মনে নিজে থাকতেই ভালোবাসি। কারো জন্য ভাবতে চাইনে, আমার জন্যও কেউ ভাবে তা পছন্দ করিনে। চিরকালের খ্যাপা আমি। সেই খ্যাপামি আমার গেল না কোনোকালেই। আমার নামই ছিল বোম্বেটে। দুরন্তও ছিলুম, আর যখন যেটা জেদ ধরতুম সেটা করা চাই-ই। তাই সবাই আমার ওই নাম দিয়েছিলেন। রবিকারাও চিরকাল ওই ‘খ্যাপা’ ‘পাগলা” বলে আমাকে ডাকতেন। আমিও যেন তাদের কাছে গেলে ছোট্ট ছেলেটি হয়ে যেতুম। এই সেদিনও রবিকাদের কাছে গেলেই আমার বয়স ভুলে আমি যেন সেই পাগলা খ্যাপা হয়ে যেতুম। তাঁরাও আমায় সেইভাবেই দেখতেন। কিছুকাল আগে যখন সস্ত্রীক শান্তিনিকেতনে এসেছিলেম, রবিকার হুকুমে প্রতিমা ও কারপ্লেজ, ওরা মিলে আমার থাকবার জন্য ঘর সাজিয়েছে যেন একটা বাসরঘর। আমি আবার আস্তে আস্তে সব তুলে রাখি, কি জানি কোন্টা ময়লা হয়ে যাবে। নিজের বিছানাপত্র খুলে নিই। সকালে উঠেই আমাকে এই বকুনি, ‘না, ও সব তুমি কি করছ।’ বলে আবার সেইভাবে ঘরদোর সাজিয়ে দেওয়ালেন।
জ্যোতিকাকার কাছে রাঁচিতে গেলুম, তখন তো আমি কত বড়, ছেলেপুলে নাতিনাতনি আমার চারদিকে। জ্যোতিকাকামশায় রোজ সকালে টুং টুং করে রিক্শ বাজাতে বাজাতে বেড়িয়ে ফিরতেন। কোলের উপর একটি কেকের বাক্স। রিক্শ থেকে নেমে কেকের বাক্সটি আমার হাতে দিয়ে বলতেন, ‘অবন, তোমার জন্য এনেছি, তুমি খেয়ো।’ ঘর ভরতি নাতিনাতনি, সে সব ফেলে আমার জন্য নিজের হাতে বাজার থেকে কেক কিনে আনলেন। এনে আমার হাতে দিয়ে বারে বারে বললেন, ‘তুমি খেয়ো কিন্তু, তোমার জন্যই এনেছি।’ আমি মহা অপ্রস্তুতে পড়তুম। বলতুম, ‘আপনি কেন কষ্ট করতে গেলেন, চাকরদের বললে তারাই তো এনে দিতে পারত।’ কিন্তু তা হবে না। ছোট ছেলেকে লজেঞ্জুস খেতে যেমন দেয়, অবন কেক খেতে ভালোবাসে, নিজের হাতে এনে দিতে হবে। এমনিই ছোট্টটি করে দেখতেন ওঁরা আমাকে চিরকাল। এখনো এক-একদিন আমি স্বপ্ন দেখি যেন বাবামশায় ফিরে এসেছেন, আর আমি ছোট্ট বালকটি হয়ে গেছি। একেবারে নিশ্চিন্ত। আনন্দে ভরপুর হয়ে যাই স্বপ্নেতে। এ স্বপ্ন আমি প্রায়ই দেখি। মা পিসিমারা সব বাড়িতে আছেন, আমিও বড় এই রকমই আছি, ছেলেপুলে সব ঘর ভরতি। বাবামশায় যেন কোথায় গিয়েছিলেন, ফিরে এলেন; বাড়ি একেবারে জমজমাট, সবাই ব্যস্ত। আমি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছি, যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, বাবামশায় এসেছেন আর কোনো ভাবনা নেই। কিন্তু বাবা যেন দু-দিন বাদেই চলে যাবেন, একটা বৈরাগ্য ভাব। স্বপ্নে ওরই বেদনা বেজে ওঠে বুকে, ঘুম ভেঙে যায়। আমার বাবা ছিলেন অজাতশত্রু; কি তাঁর মন, কি তাঁর ব্যবহার। তাঁর কাছে যে-কেউ আসত তাদের আর দুঃখ বলে কিছু থাকত না। এমনিই আনন্দময় তার সান্নিধ্য ছিল। জ্যেঠামশায়ের একটা কবিতা মনে পড়ল। তার এক লাইনেই আমার বাবামশায় আর জ্যোতিকাকামশায়ের চরিত্র ফুটে উঠেছে। জ্যেঠামশায় লিখেছিলেন—
ভাতে যেথা সত্যহেম মাতে যথা বীর
গুণজ্যোতি হরে যেথা মনের তিমির।
এ অতি সত্যিকথা। তাদের কাছে এলে মনের সব তিমির দূরে চলে যেত। আনন্দময় করে রাখতেন চারদিক। উৎসব, আনন্দ, প্রাণখোলা হো-হো হাসি, সে যে না শুনেছে বুঝবে না। অমন হাসতেই শুনিনে আর কাউকে। বাবামশায় আর জ্যোতিকাকামশায়ের খুব ভাব ছিল। একসঙ্গে তারা আর্ট স্কুলে ভরতি হয়েছিলেন। আমি যখন আর্ট স্কুলে যাই, সে রেকর্ড খুঁজে বের করি।
বাবামশায়ের মত বন্ধুভাগ্য এ বাড়ির আর কারো ছিল না। রবিকা বন্ধু পেয়েছেন, কিন্তু অবন্ধুও পেয়েছেন ঢের। বাবামশায় দেশ বেড়াতে খুব ভালোবাসতেন। থেকে থেকেই পশ্চিমের দিকে ঘুরে আসতেন। ওঁর খুব প্রিয় জায়গা ছিল অমৃতসর। অমৃতসরে গোল্ডেন টেম্পলের সামনে অনেকক্ষণ অবধি বসে থাকতেন আর মন্দিরে ভোগ দিতেন। অমৃতসরের মন্দিরের সব লোকেরা বাবামশায়কে চিনত, হোটেলের খানসাম বাবুর্চিরা অবধি। একবার বড়দাদারা অমৃতসর যান, যে হোটেলে বাবামশায় থাকতেন সেই হোটেলেই তাঁরা উঠেছেন। হোটেলের এক বুড়ো বাবুর্চি তাঁদের জিজ্ঞেস করলেন, বাবামশায়ের নাম করে যে সেই বাবু কোথায়? তিনি যখন পশ্চিমে ওই রকম ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন আমরা তখন আর কতটুকুই বা, কিন্তু আমাদের কাছে নিয়মমত চিঠি দিতেন। শুধু চিঠি দেওয়া নয় আমাদের চিঠি লেখা শেখাতেন। কি ভাবে লিখতে হবে, কোথায় কি ভুল হল চিঠি লিখে লিখে সব ঠিক করে দিতেন। চিঠি লেখা দস্তুরমত শিক্ষা করতে হয়েছে আমাদের। বাড়িতে এক পণ্ডিত আসত তার কাছেও আমাদের চিঠি লেখার শিক্ষা হত। বাবামশায় আমাদের আবার লিখতেন কার কি চাই জানাতে। একবার তিনি তখন দিল্লি আগ্রার দিকে। সেই হিন্দুমেলাতে যে দিল্লির মিনিয়েচার দেখেছিলুম সেই ছিল আমার মনে। আমি লিখলুম, আমার জন্য আগ্রা দিল্লির ছবি আনতে। বাবামশায় ফিরে এলেন; দাদারা যে যা চেয়েছিলেন, বোধ হয় ভালো ভালো জিনিসই হবে, সবাই সবার ফরমাশমাফিক জিনিস পেলেন। আমার জন্য বের হল একটা কাগজের তাড়া। আমি ভেবেছিলুম যে, হিন্দুমেলায় দিল্লির মিনিয়েচারের মত কিছু একটা হবে। কাগজের তাড়া খুলে দেখি আগ্রা দিল্লির কতকগুলো পট। সাদা কাগজের উপরে যেমন কালিঘাট লক্ষ্ণৌয়ের পট হয় সেই রকম হাতে লেখা আগ্রা দিল্লির ছবি আঁকা। এখন আর সে সব পট পাওয়াই যায় না। সেগুলি থাকলে আজ খুব দামি জিনিস হত। তখন কি আর করি, তা-ই খুলে খুলে দেখলুম, কয়েকদিন বাদে ছিঁড়ে কুটে কোথায় উড়িয়ে দিলুম। জানি কি তখন সে সব জিনিসের মূল্য!
বাবামশায় আমার কথা বলতেন, ‘ওকে আর বিদেশে পাঠাব না। ও আমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ভারতবর্ষ দেখবে, ভারতবর্ষ জানবে। এদেশটাই ওকে দেখাব ভালো করে।’ তাই হল, বাবামশায় মারা গেলেন, আমার আর বিদেশ যাওয়া হল না, এখনও ভারতবর্ষকেই দেখছি, জানছি। বড় হবার পরে যখন ছবি আঁকা নিয়েই মেতে রইলুম, মার মনে বড় ভাবনা হল যে, এই ছেলেটার লেখাপড়াও হল না বিষয়কর্মও শিখল না, কিছুই হল না। তার পর যখন দিল্লির দরবার থেকে সোনার মেডেল এল, আর্টস্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল হলুম, চারদিকে নাম রটতে লাগল, তখন মা বললেন, ‘আমি ভয় পেয়েছিলুম যে কিছুই তোর হল না। এখন মনে হচ্ছে যে কিছু একটা হলি তবুও।’
সুমধুর স্মৃতি তেমন ছিল না জীবনে। তবে কবির সঙ্গ পেয়েছি, সেই ছিল জীবনের একটা মস্ত সম্পদ। মাও বুঝতেন, বলতেন, ‘রবির সঙ্গে আছিস, বড় নিশ্চিন্ত আমি।’
১১. কর্মজীবন বলে আমার কিছু নেই
কর্মজীবন বলে আমার কিছু নেই, অতি নিষ্কর্মা মানুষ আমি। নিজে হতে চেষ্টা ছিল না কখনো কিছু করবার, এখনো নেই। তবে খাটিয়ে নিলে খাটতে পারি, এই পর্যন্ত। তাই করত, আমায় সবাই খাটিয়ে নিত। বাড়িতে কোনো ক্রিয়াকর্ম হলে সহজে হাত লাগাতুম না কিছুতে। কিন্তু যদি কোনো কাজের ভার পড়ত ঘাড়ে নিঁখুত করে সেই কাজ উদ্ধার করে দিতুম। হ্যাভেল সাহেব বসিয়ে দিলেন আর্ট স্কুলে। ছাত্র ধরে দিলেন সামনে, বললেন, ‘আঁকো, আঁকাও।’ তার মধ্যে আর একটা মানেও ছিল। বলতেন অনেক সময়েই যে, ‘ভালো ঘরের ছেলেরা যদি আর্টের দিকে ঝোঁকে পাবলিকের নজর পড়বে এদিকে। দেশের লোক তোমাদের কথায় বেশি আস্থা রাখবে।’ নেহাত মিছে বলতেন না। নয় তো তখনকার আর্ট স্কুল সম্বন্ধে লোকের ধারণাবদলাত না।
আর্ট সোসাইটি খুলে উডরফ ব্লান্টও খাটিয়ে নিতেন আমায়।
রাজা এলেন, ময়দানে মস্ত প্যাণ্ডেল তৈরি হল, রাজার বসবার মঞ্চ উঠল। উডরফ বললেন, ‘মঞ্চের চারদিকে তোমায় এঁকে দিতে হবে।’ পি. ডাবলিউ. ডির লোকেরাই ফ্রেমে কাপড় লাগিয়ে সব ঠিকঠাক করে এসে ধরলে সামনে। লাগিয়ে দিলুম ছাত্রদের, নিজেও হাত লাগালুম; হয়ে গেল মঞ্চ ডেকোরেশন। রাজার সিম্বল্ দিয়ে ছবি এঁকে দিয়েছিলুম, খুব ভালো হয়েছিল। হাজার বারোশো টাকাও পাওয়া গিয়েছিল। পরে রাজা চলে গেলে সেই ছবিগুলো বর্ধমানের রাজা কিনে নিলেন ছ-শো টাকা দিয়ে, নিয়ে তাঁর কোন্ এক ঘর সাজালেন। আমাদের ভালোই হল। এ-হাতেও টাকা পেলুম ও-হাতেও টাকা পেলুম, সব টাকা ভাগাভাগি করে বেঁটে দিলুম ছাত্রদের। আমাকে দিয়ে খাটিয়ে নিলে কোমর বেঁধেই লাগতুম, কাজও ভালো হত। আসলে ভিতরে তাগাদাও ছিল কিনা একটা। তবে না করিয়ে নিলে ছবিও আমার হত না বোধ হয়। বড় কুঁড়ে স্বভাব আমার ছেলেবেলা থেকেই; কোথাও নড়তে পর্যন্ত ইচ্ছে করে না। অথচ দেখতুম তো চোখের সামনে রবিকাকে; তিনিও তে৷ আর-এক আর্টিস্ট, পৃথিবীর এ-মাথা ও-মাথা ঘুরে বেড়িয়েছেন। বলতেন, ‘অবন, তুমি কী? একটু ঘুরে বেড়িয়ে দেখো চারদিক, কত দেখবার আছে।’ ছেলেবেলায় কল্পনা করতুম বড় হয়ে কত দেশবিদেশ বেড়াব, ইচ্ছেমত এখানে ওখানে যাব। কিন্তু বড় হয়ে যখন বেরোবার বেড়াবার সেই সময়টি এল হাতে তখন বাড়িতেই বসে রইলেম একেবারে ঘোরো বাবুটি বনে, তোমার জন্য ঘরোয়া কথার মালমশলা সংগ্রহ করতে। তবে ঘরে বসেই সারা পৃথিবীর মানুষের আর্ট আমি চর্চা করেছি, এ কথা বিশ্বাস করো।
আর্টস্কুলের চৌকিতে বসে থাকতুম; কত দেশবিদেশ থেকে নানারকম ব্যাপারী আসত নানারকম জিনিস নিয়ে। গবর্মেন্টের টাকায় আর্ট গ্যালারির জন্য জিনিস সংগ্রহ করছি, সঙ্গে সঙ্গে দেশের আর্টের সঙ্গে পরিচয়ও ঘটে যাচ্ছে। এই করে আমি চিনেছিলেম দেশের আর্ট। তার উপরে ছিলেন আমার হ্যাভেল গুরু। এ দেশের আর্ট বুঝতে এমন দুটি ছিল না, রোজ দুঘণ্টা নিরিবিলি তাঁর পাশে বসিয়ে দেশের ছবি, মূর্তির সৌন্দর্য, মূল্য, তার ইতিহাস বুঝিয়ে দিতেন। হুকুম ছিল আপিসের চাপরাসিদের উপর ওই দু-ঘণ্টা কেউ যেন না এসে বিরক্ত করে।
সদ্গুরু পাওয়ে, ভেদ বাতাওয়ে,
জ্ঞান করে উপদেশ,
তব্, কয়লা কি ময়লা ছোটে
যব্ আগ্ করে পরবেশ।
ভাবি সেই বিদেশী গুরু আমার হ্যাভেল সাহেব অমন করে আমায় যদি না বোঝাতেন ভারতশিল্পের গুণাগুণ, তবে কয়লা ছিলেম কয়লাই হয়তো থেকে যেতেম, মনের ময়লা ঘুচত না, চোখ ফুটত না দেশের শিল্পসৌন্দর্যের দিকে।
ভারতের উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম সবদিকে ছিল চর আমাদের। এক তিব্বতী লামা ছিল, মাঝে মাঝে আসত; দামি দামি পাথর, চাইনিজ জেড, তিব্বতী ছবি, নানারকম ধাতুর মূর্তি আনত। সে এলেই আমরা উৎসুক হয়ে থাকতুম দেখতে এবারে কি এনেছে। একবার এল সে বললে, শরীর খারাপ, দেশে যাব কিছুকালের জন্য। বোম্বে যাচ্ছি, কিছু টাকা পড়ে আছে, তুলতে পারি কিনা দেখি। এবারে তাই বেশি কিছু আনতে পারিনি। তবে কিছু কানুরের পুঁথি এনেছি এই দেখুন।’ খুব পুরানো পুঁথি, দুষ্প্রাপ্য জিনিস, কিন্তু আমার তো কোনো কাজে লাগবে না। এ পুঁথি আমি নিয়ে কি করব। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে হরিনাথ দে মস্ত ভাষাবিদ, সব ভাষাই তিনি জানতেন শুধু চীনে ছাড়া; বলতেন, ‘এবারে চীনেভাষাটা আমার শিখতে হবে।’ তার কাছে যেতে বললুম এই পুঁথি নিয়ে। বেশ দাম দিয়েই রাখবেন, দরকারি জিনিস। বললুম, ‘আর কি এনেছ দেখাও।’ সে একটি ছোট্ট পলার গণেশ বের করলে। বেশ গণেশটি; পছন্দ হল। পাঁচ-সাত টাকা চাইলে বোধ হয়, তা দিয়ে গণেশটি আমি পকেটে পুরলুম। বললুম, ‘আর?’ সে এবারে একটি কৌটাে বের করলে, বললে, ‘আর কিছু নেই সঙ্গে এবারে।’ সেটি একটি নাসদান, খোদাই করা স্টীলের উপরে সোনার কাজ, একটা ড্রাগন আঁকা, বড় সুন্দর। রাখবার ইচ্ছে আমার। জিজ্ঞেস করলেম, ‘দাম?’ সে বললে, ‘পঞ্চাশ টাকা।’ আমি বললুম, ‘এ বড় বেশি চাইলে।’ সে বললে,‘ তা এখন ওটা আপনার কাছেই থাক্। কেউ নেয় তো বেচে দেবেন। আমি ফিরতি পথে এসে টাকা নিয়ে যাব।’ ব’লে তাড়াতাড়ি জিনিসপত্তর গুটিয়ে চলে গেল। সে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার কি রকম যেন মনে হল, জিনিসটা রাখলুম, দাম দিলুম না, বললে ওর শরীর খারাপ—যদি ও ফিরে না আসে আর? কাজটা কি ভালো হল? যাক, কি আর করা যাবে? বাড়ি এসে অলকের মাকে পলার গণেশটি দিলুম, বললুম, ‘এটি দিয়ে আমার জন্য একটি আংটি করিয়ে দিয়ো।’ সে আংটি আমার আঙুলে অনেকদিন ছিল, পরে হারিয়ে গেল। আর নাসদানিটি তাঁর হাতে দিয়ে বললুম, ‘এটি গচ্ছিত ধনের মত সাবধানে রেখো। ওকে টাকা দেওয়া হয়নি এখনো।’
তার পর এক বছর যায়, দু-বছর যায়, আর সে আসে না। হঠাৎ একদিন সেই লামার একটি ভাই এসে উপস্থিত। বললে, ‘সে সেবারে বোম্বে গিয়ে দু-চারদিন পরেই মারা গেছে। আপনাদের কাছে তার যা পাওনা আছে সেই সব টাকা আমায় দিন।’ আমি জানতুম, এই ভাইয়ের সঙ্গে লামার বনিবনাও ছিল না। বাড়িঘরের সুখদুঃখের কথা প্রায়ই বলত সে। এখন সেই ভাই তার মৃত্যুর পরে কাগজপত্ৰ হাত করে টাকাও আত্মসাৎ করবার চেষ্টায় আছে। আমি তো তখনি তাকে হাঁকিয়ে দিলুম। বললুম, ‘কে তুমি। তোমায় জানিনে, শুনিনে, টাকা দিতে যাব কেন? যদি তোমার ভাইয়ের ছেলেপুলে থাকে বা তার স্ত্রী আসে তবে দেখতে পারি।’ সে তাড়া খেয়ে ভাগল।
তার কিছুদিন পরে সেই লামার বুড়ি স্ত্রী এল, পাহাড়ি মেয়ে। আগেও দেখেছি তাকে দু-একবার লামার সঙ্গে। সে এসেই তো খুব দুঃখ করলে তার স্বামীর জন্যে। বেচারা দেখতেও পায়নি শেষ সময়ে। তারও শরীর অসুস্থ ছিল। এতদিন তাই আসতে পারেনি। স্বামী নানা দেশবিদেশে জিনিসপত্তর বিক্রি করত, নানা জায়গায় টাকা পড়ে আছে তার। ‘বললুম, কদিন আগে তার ভাই এসেছিল যে টাকার জন্য। আমি দিইনি।’ সে বললে, ‘তা দাওনি, বেশ করেছ। আমি এসেছি তোমাদের কার কাছে তার কি জিনিসপত্তর আছে সেই খোঁজে। তোমার কাছে তো সে খুব আসত, তুমি জানো, কোথায় কি দিয়ে গেছে শেষবার।’ আমি বললুম, ‘শেষবারে সে কতকগুলি কাঞ্জুরের পুঁথি এনেছিল। আমি তাকে হরিনাথ দের কাছে পাঠিয়েছিলুম। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলুম, তিনি সেই পুঁথিগুলি খুব দাম দেবেন বলেই রেখেছিলেন। সেও ফিরে এসে নেবে বলে চলে যায়। তুমি সেখানে গিয়ে খোঁজ করো, পাবে। সে বললে, ‘আমি গিয়েছিলেম সেখানে, কিন্তু তারা কেউ সে পুঁথির সন্ধান দিতে পারেনি। হরিনাথ দে মারা গেছেন। পুঁথি যে কি হল কেউ জানে না।’ বহু পরে আমি সেই পুঁথি দেখি সাহিত্য-পরিষদে। দেখেই চিনেছি—আমার হাত দিয়ে গেছে পুঁথি, আর আমি চিনব না! যাক সে কথা, মেয়েটি তো তার দাম বা সন্ধান কিছুই পেলে না। আমি বললুম, ‘আমাকে দিয়ে গিয়েছিল সেবারে সে এই আংটির পলাটি, এটির দাম আমি তাকে দিয়েছি। আর দিয়েছিল একটি নাসদানি, দাম নেয়নি, ফিরতি পথে নেবে বলেছিল; কিন্তু সে তো আর এল না এ পথে, তুমি সেটা নিয়ে যাও।’ শুনে বুড়িটি অনেকক্ষণ চোখ বুজে চুপ করে রইল। পরে বললে, ‘আমি তো সব জানি। সেই নাসদানিটি একবার দেখতে চাই। দেখাবে?’ বললুম, ‘তা তো এখানে নেই, বিকেলে আমার বাড়িতে এসো তাহলে।’ বাড়ি সে চিনত।
বিকেলে এল, আমিও ফিরেছি কাজ সেরে। অলকের মা সিন্দুকে তুলে রেখেছিলেন কৌটােটি, তাঁকে বললুম, ‘বের করে দাও ওটি, এতদিন পরে তার মালিক এসেছে।’ কৌটোটি এনে দিলুম বুড়ির হাতে। বললুম, ‘সে পঞ্চাশ টাকা চেয়েছিল, তখন অত দাম দিতে চাইনি। তা তুমি এখন অভাবে পড়েছ যা চাইবে দেব। নয় তোমার জিনিস তুমি ফিরিয়ে নাও। তাতেও আমি অসন্তুষ্ট নই।’ বুড়ি বললে, ‘হ্যা, এ-জিনিসটি দেখেছি তার কাছে।’ বলে দু হাতে তা নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যত দেখছে আর দু চোখের ধারা বয়ে যাচ্ছে। বেচারার হয়তো স্বামীর কথা মনে পড়েছিল, কি স্মৃতি ছিল তাতে সেই জানে। খানিক দেখে কৌটোটি আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললে, “তিনি তোমায় দিয়ে গেছেন, এটি তোমার কাছেই থাকুক। দাম আমি কিছুই চাইনে।’ বললুম, ‘সে কি কথা। তোমার স্বামী মারা গেছে, তোমার টাকার দরকার, আর তুমি দাম নেবে না, বল কি? সে হবে না।’ বুড়ি ছলছল চোখে বললে, ‘বাবু, ও কথা বোলো না। আমি জানি আমার স্বামী অনেককেই নানা জিনিস বিক্রি করত, অনেকের কাছে টাকা পড়ে থাকত। আমি কলকাতায় এসে কদিন যাদের যাদের ঠিকানা পেয়েছি তাদের কাছে ঘুরেছি, দাম দেওয়া দূরে থাকুক, কেউ স্বীকার পর্যন্ত করলে না যে তারা আমার স্বামীকে চিনত। এক তুমি বললে যে, আমার স্বামীর জিনিস তোমার কাছে আছে। তোমার কাছ থেকে আমি এক পয়সাও চাইনে, এই কৌটাে তোমার কাছেই থাকুক। আর এই চাদরটি তোমার স্ত্রীকে দিয়ো আমার নাম করে।’ বলে থলে থেকে একটা মোটা সুজনির মত চাদর, পাহাড়ি মেয়েরা গায়ে দেয়, তা বের করে হাতে দিলে। জীবনের কর্মের আরম্ভে বড় পুরস্কার পেলুম আমরা দুজনে এক গরিব পাহাড়ি বুড়ির কাছে—একটি গায়ের চাদর, একটি সোনার নাসদান।
আর একবার হঠাৎ একটা লোক এসে উপস্থিত আমার কাছে—জাপানী টাইপ, কালো চেহারা, চুল উস্কোখুস্কো, ময়লা কোট পাজামা পরা, অদ্ভুত ধরনের। আর্টস্কুলের আপিসে বসে আছি, চাপরাসি এসে বললে, ‘হুজুর, এক জাপানী কুছ লে আয়া।’ বললুম, ‘আনো তাকে এখানে।’ সে এল ভিতরে, বললুম, ‘আমার কাছে এসেছ? তা কি দরকার তোমার?’ সে এদিক ওদিক তাকিয়ে কোটের বুকপকেট থেকে কালো রঙের চামড়ার একটা ব্যাগ বের করলে, করে তা থেকে দুটি বড় বড় মুক্তো হাতে নিয়ে আমার সামনে ধরলে। দেখি ঠিক যেন দুটি ছোট আমলকী। এত বড় মুক্তো দেখিনি কখনো। এ কোথায় পেল? সে মুক্তো দুটিকে শঙ্খমণি না কি মণি বলে, আর আমার চোখের সামনে নাড়ে। বললুম, ‘বিক্রি করবে?’ দাম চাইলে দুটােতে একশো টাকা। মুক্তো কিনব, তা নিজে তে চিনিনে আসল নকল। বাড়িতে ফোন করে দিলাম জহুরী কিষণচাঁদকে বড়বাজার থেকে খবর দিয়ে যেন আনিয়ে রাখে, আমি আসছি এখনি। ভুল হয়ে গেল গাড়িটার কথা বলতে। বাড়ির গাড়ি আসবে স্কুল ছুটি হলে। . আমার আর ততক্ষণ সবুর সইছে না। একটা ঠিকে গাড়ি করেই রওনা হলুম সেই লোকটিকে নিয়ে। বাড়ি পৌঁছে দেখি কিষণচাঁদও এসে উপস্থিত। কিষণচাঁদকে সেই মণি দুটাে দেখালুম, বললুম, ‘দেখো তো, একশো টাকা দাম চাইছে। বলে শঙ্খমণি, তা আসল কি নকল দেখে দাও, শেষে না ঠকি যেন।’ মনে পড়ল দাদা একবার পাহাড়ে এইরকম বড় মুক্তো কিনে খুব ঠকেছিলেন। মুক্তো কিনে কার কথা শুনে লেবুর রস দিয়ে যেই না ধুয়েছেন মুক্তোর উপরের এনামেল উঠে গিয়ে ভিতরের সাদা কাঁচ বেরিয়ে পড়ল, ঠিক যেন দুটি সাদা মার্বেল। বললুম, ‘দেখো কিষণচাঁদ, আমারও না আবার সেই অবস্থা হয়।’ কিষণচাঁদ অনেকক্ষণ মুক্তো দুটি হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলে, বললে, ‘ঠিক বুঝতে পারছিনে।’ আমারও মন খুঁত খুঁত করতে লাগল। যে কাজে মনে খুঁত থাকে তা না করাই ভালো। আমি বললুম, ‘থাক্ কিষণচাঁদ, বুঝতে যখন পারছ না তুমি, এ ফেরত দিয়ে দেওয়াই ভালো। দরকার নেই রেখে এ জিনিস।’ মণি দুটাে ফেরত দিয়ে দিলুম, সেই লোকটা চলে গেল। তার কিছুদিন পরে কাগজে দেখি, বিলেতের কোন এক বড়লোকের মেমের একটা নেকলেস হারিয়েছে, বড় বড় মুক্তো ছিল তাতে। পরে বাড়ির ছেলেদের ডেকে বলি, ‘ওরে দেখ্ দেখ্ না রেখে ভালোই করেছি। কি জানি হয়তো সেই মুক্তোই এনেছিল বিক্রি করতে। শেষে চোরাই মাল রেখে মুশকিলে পড়তে হত হয়তো। লোকটার ঠিক চোর-চোর চেহারাই ছিল।’
আর্টিস্ট হচ্ছে কলেক্টর, সে এটা ওটা থেকে সংগ্রহ করে সারাক্ষণ, সংগ্রহেই তার আনন্দ। রবিকা বলতেন, ‘যখন আমি চুপ করে বসে থাকি তখনই বেশি কাজ করি।’ তার মানে, তখন সংগ্রহের কাজ চলতে থাকে। চেয়ে আছি, ওই সবুজ রঙের মেহেদি-বেড়ার উপর রোদ পড়েছে। মন সংগ্রহ করে রাখল, একদিন হয়তো কোনো কিছুতে ফুটে বের হবে। এই কাঠের টুকরোটি যেতে যেতে পথে পেলুম, তুলে পকেটে পুরলুম। বললে তো ঝুড়ি ঝুড়ি কাঠের টুকরো এনে দিতে পারে রথী ভাই এখখুনি। কিন্তু তাতে সংগ্রহের আনন্দ থাকে না। এমনি কত কিছু সংগ্রহ হয় আর্টিস্টের মনের ভাণ্ডারেও। এই সংগ্রহের বাতিক আমার চিরকালের।
যাক সেবার তো মুক্তো ফসকে গেল। কিন্তু কি করে জিনিস হাতে এসে পড়ে দেখো। একখানি পান্না, ইঞ্চিখানেক চওড়া, চৌকো পাথরটি, দেখেই চোখে পড়ে, উপরে খোদাই করা মোগল আমলের। আজকাল এ জিনিস পাবে না কোথাও। বুড়ো রোগা অনন্ত শীল জহুরী, পুরানো পাথর বিক্রি করে। ভালো কিছু হাতে এলেই নিয়ে আসে আমাদের কাছে। একদিন নিয়ে এল কয়েকটা পুরোনো টিনের কৌটোভরা নানারকমের পাথর। তার মধ্যে ওই পান্নাটি দেখেই আমার কেমন লোভ হল। তাড়াতাড়ি হাতে তুলে নিলুম। বললুম, ‘এটি কত হলে দেবে? টাকা পঞ্চাশেক হলে চলবে তো?’ বুড়ো জহুরী ঘাগি লোক; চোখ দেখেই বুঝেছিল, জিনিসটি খুবই পছন্দ হয়েছে আমার। দাম বাড়াবার ইচ্ছে না কি? বললে, ‘তা আমি ঠিক করে এখন বলতে পারছিনে। পরে জানাব।’ এই বলে সেদিন সেটি নিয়ে চলে গেল। মনটা আমার খারাপ হয়ে গেল, বড় সুন্দর পান্নাটি ছিল। লোভও হয়েছিল খুব রাখবার, নিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। তা কি আর করব। গেল তো গেল। বুড়োর আর দেখা নেই।
মাস ছয়েক পরে তার ছেলে এল একদিন, নেড়া মাথা। বললে, ‘বাবা চলে গেছেন।’ বললুম, ‘সে কি রে। এই যে সেদিনও এসেছিল পুরোনো পাথর নিয়ে। তা তুই এখন কি করছিস?’ সে বললে, ‘আমিই বাবার দোকান দেখাশুনো করি। আপনারা আমার কাছ থেকে পাথর মণি মুক্তো কিনবেন না কিছু? বরাবর তো বাবাই আপনাদের দিতেন এসে যা চাইতেন। আমার কাছ থেকেও তেমনি নেবেন দয়া করে।’ তাকে বললুম, ‘দেখ্, শেষবার তোর বাবা এনেছিলেন একটি পান্না। আমার পছন্দ হয়েছিল, দামও বলেছিলুম পঞ্চাশ টাকা। কয়েকদিন বাদে সে আসবে বলে গেল, আর তো এলো না। সেই পাল্লাটি আমায় এনে দিতে পারিস?’ পুরোনো খদ্দের হাতে রাখবার বাসনা, পরদিন দেখি ছেলেটি ঠিক খুঁজেপেতে নিয়ে এল সেই পান্নাটি একটি মরচে পড়া টিনের কৌটোয় পুরে। বললুম, ‘দাম কত চাস?’ সে বললে, ‘বাবার সঙ্গে যা কথা হয়েছে তাই দেবেন।’ টাকা নিয়ে সেদিন সে চলে তো গেল। ছেলেমানুষ পান্নার মূল্য বোঝেনি হয়তো। কয়েকদিন বাদে কার সঙ্গে কি কথা হয়েছে, সে এসে হাজির। বললে, ‘একটি ভুল হয়ে গেছে।’ বললুম, ‘আর ভুল। দস্তুরমত পান্নাটি কিনেছি আমি। রসিদ দিয়ে তুমি টাকা নিয়েছ। এখন ভুল বললে শুনব কেন? এই পান্নাটি তোমার বাপের কাছে চেয়েছিলুম সেবারে, পেলুম না। হাতছাড়া হয়ে গেল, আশা তো ছেড়েই দিয়েছিলুম আমি। এবারে তোমার কাছ থেকে আমি কিনেছি, আর কি হাতছাড়া করি? সে চলে গেল। তারপর বোম্বের ঠাকুরদাস জহুরী আসতে তাকে পান্নাটি বের করে দেখাই। সে তো হাতে নিয়ে অবাক । বললে, ‘এ জিনিস আপনি পেলেন কোথায়? এ যে অতি দুর্লভ পান্না, বহুমূল্য জিনিস। এইরকম ফুল-খোদাইকরা পান্না মোগল আমলেই ব্যবহার হত শুধু। ঠাকুরদাস বললেন, এর এক রতির দাম পাঁচশো টাকা। পান্নাটির ওজন হল বেশ কয়েক রতি। বললে, ‘আপনি পঞ্চাশ টাকায় কিনেছেন আমি এখনি ছশো টাকা দিতে রাজি আছি এটির জন্য।’
সেই পান্নাটি, আর একটি দুর্লভ মোহর ছিল আমার কাছে, তার একদিকে জাহাঙ্গীর আর একদিকে নূরজাহানের ছবি। রাখালবাবু দিয়েছিলেন আমায়, একশো টাকা দিয়ে কিনেছিলুম। এই মোহর আর পান্নাটি দিয়ে একটি ব্রোচ তৈরি করালুম আমাদের বিশ্বস্ত জহুরীকে দিয়ে। সেই পাল্লাটির চারদিকে ছোট ছোট মুক্তো, আর মোহরটি ঝুলছে পান্নাটির নিচে। ব্রোচটি অলকের মাকে দিলুম। তিনি প্রায়ই কাঁধের উপরে ব্যবহার করতেন সেটি, বেশ লাগত। সেই একবার খুব পান্নার বাতিক হয়েছিল।
ভেবেছিলুম খুঁজতে খুঁজতে কোহিনুর-টােহিনুর পেয়ে যাব হয়তো একদিন। পেলুম না। কিন্তু তার চেয়েও বেশি আজকাল আমার এই কাঠকুটো কুটুমকাটাম—কোথায় লাগে এর কাছে কোহিনুর মণি। আমার ফটিকরানী, কোনো কোহিনুর দিয়ে তৈরি হবে না। ভাঙা ঝাড়ের কলমটি নমিতা এনে দিলে। ওডিকোলনের একটা বাক্স, সামনেটায় কাঁচ দেওয়া, তাকে শুইয়ে দিলুম সেই কাঁচের ঘরে, বললুম, ‘এই নাও আমার ফটিকরানী ঘুমোচ্ছে। রেখে দাও যত্ন করে।’ ইচ্ছে ছিল, আর একটি সবুজ রঙের কাঠি পেলে শুইয়ে দিতুম পাশাপাশি, থাকত দুটিতে বেশ।
সেই পান্নার বাতিকের সময়ে—আর একটি লোক এল একদিন, জব্বলপুরে পাওয়া যায় নানারকম পাথর, বহু পুরোনো পোকামাকড় গাছপালা পাথর হয়ে গেছে, সেই সব নিয়ে। ভারি সুন্দর সুন্দর পাথর সব। তার মধ্যে একটি ছিল ঠিক গোল নয়, বাদামের মতো গড়নটি দেখতে, রঙটি অতি চমৎকার। পছন্দ হল, কিন্তু দাম বেশি চাইল বলে রাখলুম না। লোকটি তার সব পাথর দেখিয়ে খানিক বাদে চলে গেল। বসে আছি বারান্দায় চুপচাপ। সমরদার ছোট নাতনিটি এসে সেখানে খেলা করতে লাগল। দেখছি সে খেলা করছে আর অনবরত মুখ নাড়ছে। বললুম, ‘দেখি তোর মুখে কি?’ সে সামনে এসে হাঁ করে জিব মেলে ধরলে। দেখি জিবের উপরে সেই পাথরটি। বললুম, ‘কোথায় পেলি তুই এই পাথর। দে শিগগির বের করে। গিলে ফেললে কি কাণ্ড হবে।’ এখন, সেই লোকটি যাবার সময় সব জিনিস তুলেছে, ভুলে সেই পাথরটিই ফেলে গেছে। সমরদার নাতনি সেটি পেয়ে লজেঞ্জুস ভেবে মুখে পুরে বসে আছে। তাড়াতাড়ি তার মুখ থেকে পাথরটি নিয়ে পকেটে পুরলুম। পরদিনই সেটি আমার আংটিতে বসিয়ে একেবারে আঙুলে পরে বসলুম। সুন্দর পাথরটি, তার গায়ে একটি মৌমাছি দুটি ডানা মেলে বসে আছে, পাথর হয়ে গিয়েছিল। মেয়েরা এল ছুটে দেখতে, বললুম, ‘ওরে দেখ্, তাজমহল কোথায় লাগে এর কাছে। তাজমহল? যে মরেছিল সে তো ধুলো হয়ে গেছে কবে। আর প্রকৃতি এই মৌমাছিটিকে কি করে রেখেছে যে, আজও এ ঠিক তেমনিই আছে। রঙও বদলায়নি একটু। কবে কোন্ লক্ষ লক্ষ বছর আগে বসন্ত এসেছিল এ ধরার বুকে, মৌমাছি ডানা দুটি মেলে খাচ্ছিল ফুলের মধু আকণ্ঠ পুরে, যে রসে ডুবেছিল, সেই রসের কবরে আজও আছে সে তেমনি মগ্ন হয়ে।’
আর্ট স্কুলে মাঝে মাঝে এক সন্ন্যাসী আসত। চাপরাসিরা ধরে নিয়ে আসত গাছতলা থেকে ক্লাসে মডেল করবার জন্য। আসে, মডেল হয়ে বসে, ছেলেরা আঁকে, ক্লাস শেষ হলে পয়সা নিয়ে চলে যায়। মাঝে মাঝে দেখি সন্ধ্যের দিকে বা সকালে সন্ন্যাসী হ্যাভেলের ফ্ল্যাট থেকে বের হয়। ব্যাপার কি। হ্যাভেলের মেম বলেন, ‘আর পারিনে অবনবাবু। কোন্ এক সাধু জুটেছে, সাহেব তার কাছে ধ্যান শেখে, যোগ শেখে। সারাক্ষণ কেবল ওই করছে।’ আমি বললুম, ‘এ তে ভালো কথা নয়। যত সব বাজে সাধুসন্ন্যেসীর পাল্লায় পড়ে না ঠকেন শেষ পর্যন্ত।’ একদিন বিকেলে সেই সাধু আমার আপিসঘরে এসে উপস্থিত। বললে, ‘এই নাও পাকা হরীতকী। এটি খেলে যৌবন অক্ষুণ্ণ থাকবে, বয়স বাড়বে না, চুল পাকবে না’—কত কী। বলে লাল বকুলবিচির মত একটা কি হাতে গুঁজে দিলে। সন্ন্যাসী চলে যেতে আমি সেটি পকেটে ফেলে রাখলুম। ভাবলুম খেয়ে শেষে মরি আর কি। খানিক বাদে হ্যাভেল সাহেব এলেন আমার ঘরে, বললেন, ‘সন্ন্যাসী এসেছিল তোমার কাছে? কি দিল তোমায়?’ আমি পকেট থেকে সেটি বের করে বললুম, ‘এইটি।’ সাহেব বললেন, ‘আমায়ও একটা দিয়েছিল। আমি খেয়ে ফেলেছি।’ বললুম, ‘করেছ কি তুমি? না জেনে শুনে তুমি খেলে কি বলে?’ খেয়ে ফেলেছেন, কি আর হবে। মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। বাড়ি ফেরবার পথে সেই পাকা, হরীতকী পকেট থেকে বের করে রাস্তায় ফেলে দিলুম। কি জানি চিরযৌবনের লোভ যদি বা জাগে সাহেবের মত।
এমনি কতরকম চরিত্রের লোক নজরে পড়ত তখন।
১২. হ্যাভেল সাহেবদের একটা সোসাইটি ছিল
হ্যাভেল সাহেবদের একটা সোসাইটি ছিল জনকয়েক সাহেব মেম আর্টিস্ট নিয়ে। সন্ধ্যেবেলা আর্ট স্কুলেই তারা ঘণ্টা দুয়েক কাজ করত; আলোচনা সমালোচনা হত, মাঝে মাঝে খাওয়া-দাওয়াও চলত, অনেকটা আর্ট ক্লাব গোছের। মার্টিন কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার থর্নটন সাহেবই দেখাশোনা করতেন। তাঁর উপরেই ছিল ওই আর্ট ক্লাবের সব কিছুর ভার। চমৎকার আঁকতেও পারতেন তিনি। অমায়িক সৎ লোক ছিলেন, মহৎ প্রাণ ছিল তার। অমন সাহেব দেখা যায় না বড়। আমার সঙ্গে খুব জমত। সেই থেকেই আমার সঙ্গে তার আলাপ। পরে আমাদের সোসাইটির সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন। আমি যখন আর্ট স্কুলে তিনি আসতেন আমার কাছে প্রায়ই; আবার ডেকেও পাঠাতেন কখনও কখনও। চারটের পরে যেতুম তার আপিসে। খুব বিশ্বাস ছিল আমার প্রতি, টেবিলের দেরাজ থেকে তাঁর আঁকা নানারকম স্থাপত্যকর্মের প্ল্যান বের করে আমায় দেখাতেন, পরামর্শ চাইতেন। কোন্টা কি রকম হলে আরো ভালো হয় দু বন্ধুতে মিলে বলা কওয়া করতুম। সেই সময়ে দেখেছি তার ড্রইং। ভারি সুন্দর। ভারতবর্ষের নানা জায়গা ঘুরেছেন; উদয়পুর জয়পুরের কতকগুলি স্কেচ্ করেছেন, লোভ হত দু-একখানির উপর। অনেক সাহেব এদেশের স্কেচ্ করেছে, ছাপিয়েছেও দু-একজন; কিন্তু তাদের স্কেচ্গুলিতে কেমন যেন বিদেশের ছাপ থাকত আর থর্নটনের অ্যালবাম যেন ভারতবর্ষের হুবহু ছবি। মাঝে মাঝে তার ফ্ল্যাটেও যেতুম; তেতলার ফ্ল্যাট, গোল সিঁড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে উপরে উঠে চাপরাসিকে জিজ্ঞেস করতুম, ‘সাহেব আছেন?’ চাপরাসি উত্তর দিতে না দিতেই ওদিক থেকে ঢিলে ঢালা পাজামা পরে সাহেব এসে উপস্থিত হতেন; তারপর দুজনে বসে কত গল্প, কত হাসি, কত মজাই না করতুম। প্রাণ-খোলা হাসি ছিল তার। তাদের আর্ট ক্লাব ভেঙে গেলে পর, ক্লাবের বোর্ড আলমারি আমাকে তিনি দিয়েছিলেন। বললেন, ‘কী হবে আর এসব দিয়ে, তুমিই নিয়ে যাও, কাজে লাগবে।’
আমাদের আর্ট সোসাইটির উনি একজন বড় উৎসাহী সভ্য ছিলেন। শুধু তাই নয়, বড় খদ্দেরও ছিলেন। নন্দলালের অনেক ছবি উনি কিনেছেন। একবার নন্দলালের ‘সতী’ ছবিখানি কিনেছেন। সে সময়ে আমরা ঠিক করি, ভালো ভালো ছবিগুলি ছাপিয়ে বাজারে ছড়িয়ে দেব। করিয়েও ছিলুম কিছু, খুব ভালো হয়েছিল। তা সেই ‘সতী’ ছবিখানি ও আর খানকয়েক ছবি, ভালো করে প্যাক করে জাপানে পাঠানো হল ছাপাবার জন্য। ওকাকুরা, টাইকান, ওঁরা ব্যবস্থা করে দিলেন। ভালো কোম্পানিতে ছবিগুলি ছাপা হয়ে কিছুকাল বাদে তা ফেরত এল। থর্নটনের ‘সতী’ও এল। তিনি ছবির প্যাক খুলে ছবিটি বের করে দেখেন, ছবি আর চিনতেই পারেন না। খবর পাঠালেন, শিগগির এসো, কাণ্ড হয়ে গেছে, সতী কি রকম বদলে গেছে। সেই আগের সতী আর নেই। তাড়াতাড়ি গেলুম। কি ব্যাপার? গিয়ে দেখি তাই তো, মনে হয় আগুনে পুড়ে সতীর গায়ের রঙ যেন ছাই হয়ে গেছে। রুপো পুরানো হয়ে গেলে যেমন হয় তেমনটি। সাহেব বললেন, ‘এ কেমন হল?’ বললুম, ‘রঙ বিগড়ে গেছে। কেন গেছে তা কি করে বলব বল?’ সাহেব বললেন, ‘এ সারানো যাবে না?’ বললুম, ‘না, এ আর সম্ভব নয়।’ সাহেবের মন খারাপ, তাঁর সতীর এমন দশা হয়ে গেল। তখনকার ছবি আমরাই বেশির ভাগ কিনে রাখতুম। সতীটির উপর আমার খুব লোভ ছিল। সাহেব কিনে নিলে, কি আর করি। বললুম, ‘তুমি যদি এই ছবিটি না রাখ তবে আমায় দিয়ে দাও, তার বদলে অন্য ছবি নাও।’ সাহেব বললেন, ‘তবে তোমার ছবি দিতে হবে আমায়।’ বললুম, তা বেশ। পছন্দ কর কোন্টি নেবে।’ শেষে সাহেব ঔরঙ্গজেব দারার মুণ্ড দেখছেন যে ছবিটি ও আর-একটি ছবি এই দুখানির বদলে সতীটি আমায় ফেরত দিলেন।
বাড়ি নিয়ে এলুম সতীর ছবি। মনে মনে ভাবছি কি উপায় করা যায় এর। ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল একটা কোনো বইয়ে পড়েছিলুম খোলা হাওয়া-আলোতে রাখলে কতকগুলো রঙের জলুস ফিরে আসে। ভাবলুম, কি জানি, জিঙ্ক দিয়ে মুড়ে পাঠিয়েছিল ছবি, জিঙ্কের গরমে ও জাহাজের গুমটে মিলে কেমিক্যাল ক্রিয়ায় হয়তো রঙ বদলে গিয়ে থাকবে। বাড়িতে এসে ছবিখানি আমার শোবার ঘরে জানলার পাশটিতে টাঙিয়ে রাখলুম। পুবের আলো এসে পড়ে তাতে রোজ। রইল তো সেখানেই। কিছুদিন বাদে একদিন দেখি, সতীর রঙ ফিরে গেছে, সেই আগের রঙ এসে লেগেছে গায়ে, আলো দিয়ে যেন ধুইয়ে দিয়েছে তার পোড়া রঙ। বাঃ বাং, এ তো বড় মজা। উড্রফকে ডেকে এনে দেখাই, থর্নটনকে ডেকে এনে দেখাই। তাঁরাও দেখে অবাক। থর্নটনকে বললুম, ‘কি, লোভ হচ্ছে নাকি? কিন্তু পাবে না আর ফিরে। আমার কাছে এসে সতীদেহের রঙ ফিরে এলো, আর কি দিই তোমার হাতে তুলে?’ সাহেব শুনে হাসেন, বলেন, ‘না, এ তোমারই থাক্।
থর্নটনের মত অমন বন্ধ হয়নি আর আমার। তাঁরই চাপরাসিকে দিয়েছিলেন আমার কাছে ছবি আঁকা শিখতে। বলিনি সে গল্প বুঝি? একবার সাহেব যাবেন দেশে, চাপরাসিকে দিয়ে গেলেন আমার কাছে। বললেন, ‘এর ছবি আঁকার হাত আছে, একে তুমি ছবি আঁকা শেখাও; খরচপত্তর যা লাগে তা আমি দেব। সাহেব চলে গেলেন দেশে; পরদিন চাপরাশি এল আমার আর্ট স্কুলে। সাহেবেরই একটা লাল নীল পেনসিল দিয়ে ট্রামগাড়ি, কলকাতার রাস্তা, এই সব আঁকত অবসর সময়ে। বসিয়ে দিলুম তাকে নন্দলালের সঙ্গে। তাদের বললুম, ‘এও একজন ছাত্র, একে যেন অবজ্ঞা কোরো না। এখানে সবার আসন সমান।’ চাপরাসি দাঁড়িয়ে আছে একপাশে; বললুম, ‘বোস তুই এখানে এই বেঞ্চিতে।’ সে কেবলি কাঁচুমাঁচু করে; কিছুতেই বসতে চায় না। তাকে ভালো ভাবে বসাতেই আমার লাগল বেশ কিছুদিন। রোজই সে আসে, ছবি আঁকে। কি আর তেমন আঁকবে এই কয়দিনে, তবু হাত তার ধীরে ধীরে বেশ পাকা হয়ে আসছিল। সাহেব দেশ থেকে ফিরে এলেন, চাপরাসি আবার তার কাজে যোগ দিলে। একদিন সাহেব এসে বললেন ‘তুমি আমার চাপরাসির করেছ কি? ছবি আঁকার কথা ছেড়ে দাও, লোকটা একেবারে বদলে গেছে। তার শিষ্টতা আচারব্যবহার কথাবার্তা আমাকে মুগ্ধ করছে। আগের সেই চাপরাসি আর নেই, তুমি আগাগোড়া লোকটাকে এমন করে বদলে দিলে কি করে?’ বললুম, ‘আর কিছু নয়, আমি শুধু ওকে বসতে শিখিয়েছিলুম।’
সে সময়ে বাংলাদেশের যত জমিদার মিলে একটা সোসাইটি হয়, নাম ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন। সিংহ মশায় সভাপতি। উড্রফ আর ব্লান্টও জুটল সে সময়ে। সুরেন কোমর বেঁধে কাজ করে তাতে। সুরেনের মাথায়ই খেলল প্রথমে একটা ছবির একজিবিশন করতে হবে। আমার যা কখানা ছবি ছিল, ওকাকুরা এনেছিলেন সঙ্গে কিছু জাপানী প্রিন্ট, আর এখান-ওখান থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে জোগাড় করলে আরও কখানা ছবি। তাই নিয়ে সে তৈরি একটা মস্ত বাড়ি ছিল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের; নিচের তলায় বিলিয়ার্ড রুম, পড়বার ঘর, উপরে ব্যবস্থা আছে কোন সভ্য দূর থেকে এলে থাকতে পারে সেখানে, সুরেন চাইলে সেই বিলিয়ার্ড-রুমেই একজিবিশন হবে। সিংহ মশায় বললেন, ‘ছবির আমি বুঝিনে কিছুই; তবে চাইছ ঘর একজিবিশন সাজাতে, তা নাও।’ সেই বিলিয়ার্ড-রুমেই ছবি সব সাজানো হল। বেশ লোকজন আসত দেখতে; আমাদেরও ভাল লাগত, ইচ্ছে ছিল আরো কয়েকদিন চলে এমনি। এদিকে ছোকরা ব্যারিস্টার ছিলেন অনেক সেই অ্যাসোসিয়েশনে, নতুন বিলেতফেরত, তাঁরা রোজ সন্ধ্যেয় আসেন, বিলিয়ার্ড খেলেন, ব্রিজ খেলার আড্ডা জমান, তাঁদের হল মহা অসুবিধে। কদিন যেতে না-যেতেই তাঁরা লাগলেন গজগজ করতে, ‘ঘর আটকে রাখা হয়েছে।’ গজগজানি শুনতে পেয়ে তাড়াতাড়ি ছবি-টবি নামিয়ে নিলুম দেয়াল থেকে। সেই একজিবিশনে উড্রফ, ব্লান্ট, এঁদের সঙ্গে আলাপ জমল। সেই হল প্রথম আমাদের ছবির একজিবিশন। তার দু-তিন বছর পরে হ্যাভেল চাইলেন তাদের সেই ছোট্ট আর্ট-ক্লাবটা ভালো করে তৈরি করতে। কমিটি গঠন হল, আমরা তাতে যোগ দিলুম। ল্যাণ্ডহোল্ডার্সদেরও কেউ কেউ এলেন। উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহনও এলেন। লর্ড কিচনার সভাপতি, আমাকে হ্যাভেল বলেন সম্পাদক হতে। আমি বলি, ‘ওসব হিসেব-নিকেশে আমি নেই। পারিনে কোনোকালে।’ কিছুতেই ছাড়েন না, শেষে যুগ্ম সম্পাদক হই। জানো, বেশ কিছুকাল আমি লর্ড কিচনারের সম্পাদকগিরি করেছি। একবার এক পার্ট দিলেন ফোর্ট উইলিয়ামে। এখানে শান্ত্রী, ওখানে শান্ত্রী, বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। দেখে তো বুক আঁতকে আঁতকে ওঠে। রাস্তাও কি রকমের; গাড়ি ঘুরে ঘুরে পৌঁছল দোতলায় না তেতলায় ঠিক ওঁর ঘরটির সামনে। নানারকম জিনিসের সংগ্রহ ছিল তার। প্রায়ই যেতে হত সেখানে। এখন সেই পার্টিতে এসেছেন অনেকেই নিমন্ত্রিত হয়ে। এক রাজা বন্ধু ধরলেন, ‘আমায় লর্ড কিচনারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে হবে।’ সাহেব দেখি তখন মেমের সঙ্গে গল্পে মশগুল এক ফুলবাগানে। ভাবভঙ্গী দেখেই মনে হচ্ছে, বেশ জমে উঠেছে। ভাবলুম, দরকার নেই বাপু এখন গিয়ে, কি জানি মিলিটারি মেজাজ, দেবে হয়তো এখনি মাথাটা গুড়িয়ে। রাজ-বন্ধু এদিক থেকে কেবল খোঁচাচ্ছেনই। কি করি, একপায়ে দুপায়ে এগিয়ে গেলুম খানিকটা। সাহেব কথার ফাঁকে একবার পিছনে তাকিয়েছেন কি, রাজাকে ঠেলে দিলুম, বললুম, ‘ইনি হচ্ছেন রাজা অমুক।’ সাহেব হাত ঝাঁকুনি দিয়ে হ্যাণ্ডশেক করে বললেন, ‘Well Tagore, take him upstairs and show him my collection, please.’ রাজাকে নিয়ে চলে গেলুম সেখান থেকে। রাজা তো খুব খুশি ওইটুকু হ্যাণ্ডশেক করতে পেয়েই। যাক সেকথা। এখন এই সোসাইটির নাম কি দেওয়া যায়? কেউ কেউ প্রস্তাব করলেন অরিয়েটাল আর্ট সোসাইটি। আমি বললুম, ‘না, নাম হোক্ এর ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট। শুধু বাঙালি নয়, দুই সম্প্রদায় মিলল এতে। দাদাও ছিলেন। অনেকে স্থায়ী সভ্য হলেন। পার্ক স্ট্রীটে বাড়ি ভাড়া নেওয়া হল, আর্টিস্টরা কাজ করবে সেখানে; কেউ যদি ইচ্ছে করে থাকতেও পারে, এমন ব্যবস্থা রইল। আর্ট স্কুলের মস্ত হলে দু-তিনটে ছবির একজিবিশন হল। উড্রফ তার জাপানি প্রিন্টের কালেক্শন দিলেন। Gesiking বলে এক মেম সব ঋতুর ফুল এঁকেছিলেন দেশি ধরনে, তাও একবার দেখান হল। দেখতে দেখতে আমাদের সোসাইটি খুব জমে উঠল। মাৰ্চেণ্ট কমিউনিটি, সিভিলিয়ান কমিউনিটি, লাটবেলাট জজ-ম্যাজিস্ট্রেট রাজারাজড়া সবাই তাতে যোগ দিয়েছেন; সবাই কিছু-না-কিছু করছেন। উড্রফ ক্যাটালগ লিখতেন। তখনকার ক্যাটালগ সাহিত্য ছিল বললেই হয়। প্রতি ছবির নিচে গল্প থাকত; আমার ইংরেজি বিদ্যেয় কুলোত না, ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কোনো রকম করে লিখে দিতুম। উড্রফ তা থেকে ভালো করে লিখতেন।
দেখাদেখি অন্য আর্টিস্টরা ঠিক করলেন, তাঁরা নিজেরা একটা সোসাইটি করবেন। হরিনারায়ণ বসু ছিলেন আর্ট স্কুলের ভাইস্প্রিন্সিপাল, বরদাকান্ত দত্ত সেকেণ্ড মাস্টার, মন্মথ চক্রবর্তী যিনি বউবাজারের আর্ট স্কুল প্রথম শুরু করেন, এই কয়জন মিলে ঠিক করলেন একটা সভা করে সব ব্যবস্থা করতে হবে। কোথায় সভা হবে। আমাকেও তাঁদের দলে টানবার ইচ্ছে; ঠিক হয় আমাদের বাড়িতেই সভা বসবে। সভার সব ঠিক, খাওয়াদাওয়ারও কিছু ব্যবস্থা করা গিয়েছিল। এখন সেই সভার মধ্যেই কে কি কাজ করবে এই নিয়ে মহা তর্কাতর্কি; শেষ পর্যন্ত প্রায় তুমুল ব্যাপার। এ বলেন, ‘আমি কেন প্রেসিডেন্ট হব’, উনি বলেন, ‘অমুক থাকতে ও কাজের ভার আমার উপর কেন’ ইত্যাদি। হল না আর শেষ পর্যন্ত কিছুই, ওখানেই থেমে যেতে হল সবাইকে। আমি বললুম, ‘শুরুতেই যখন এই রকম মারামারি তখন আমি, বাপু, এর মধ্যে নেই।’ গেল ভেঙে সব স্কীম।
আমরা যে সোসাইটি করেছিলুম সে ছিল একেবারে অন্যরকমের। আমরা করেছিলুম এমন একটা সোসাইটি যেখানে দেশী বিদেশী নির্বিশেষে একত্র হয়ে আর্টের উন্নতির জন্য ভাববে, শুধু ভারতীয় নয় প্রাচ্য শিল্পের সব জিনিস দেখানো হবে লোকদের। তাতে এমন ব্যবস্থাও ছিল যার যা ব্যক্তিগত শিল্পবস্তুর সংগ্ৰহ ছিল তাও দেখানো হত। মাঝে মাঝে এক-একজনের বাড়িতে পার্টি জমত। সভ্য সবাই আসত; আমোদ-আহ্লাদ, খাওয়াদাওয়া, আর্ট সম্বন্ধে আলোচনা, সবই হত। উড্রফ পান পর্যন্ত দিতেন তাঁর বাড়িতে যখন পার্টি হত। পান, ফুলের মালাও চল হয়ে গিয়েছিল সাহেববাড়িতে সেই সময়ে। তা ছাড়া যে-দেশে যা-কিছু সুন্দর পাওয়া যায় এনে সাজিয়ে দিতুম একজিবিশন করে। সেসব একজিবিশনও হত এক বিরাট ব্যাপার। কাঁচের বাসন, কার্পেট, যেখানকার যা কিছু ভালো ভালো পুতুল, গয়না, ছবি, কিছু বাদ পড়ত না। সব বাছাই বাছাই জিনিস, যা-তা হলে আবার হবে না।
একবার এমনি এক বিরাট বার্ষিক একজিবিশনের আয়োজন হচ্ছে। উড্রফ বললেন, ‘এবারে ভারতবর্ষের সব জায়গার জিনিস জোগাড় করতে হবে।’ তিন মাস আগে থেকে জায়গায় জায়গায় চিঠি লিখে দেওয়া হল; কোথাও আমাদের লোক গেল জিনিস সংগ্রহ করতে; কোথাও বা টাকা পাঠানো হল, পার্সেল করে যেসব জিনিস আসবে তার খরচ বাবদ। কিছুদিন বাদেই নানা জায়গা থেকে ছোট বড় হালকা ভারি প্যাকিং বাক্স আসতে লাগল, সে কি উৎসাহ আমাদের বাক্স খোলার। আমাদের চতুর্দিকে সাজানো প্যাকিং বাক্স ঠাসা, একটা-একটা করে খোলা হচ্ছে। দিল্লি থেকে এসেছে সুন্দর সুন্দর পটারি; কাশ্মীর থেকে নানারকম শাল, হাতের কাজ, তার মধ্যে একটা পুরানো পেপারম্যাসের উপর কাজ করা দোয়াতদানি ছিল বড় সুন্দর, এখনো মনে পড়ে, বড় বড় কার্পেট; কেষ্টনগরের পুতুল; বোম্বে থেকে ভীষণ সব ছবি; লক্ষ্ণৌর তাস, বাদশা-বেগমের মিনিয়েচার আঁকা, বেগম-বাদশারা খেলত; উড়িষ্যার পট; আর গঞ্জাম থেকে এল তিনটি হাতির দাঁতের মূর্তি—একটি কূৰ্ম অবতার, একটি রাধাকৃষ্ণের বিহার, সবাইকে দেখাবার মত নয়, কিন্তু কি চমৎকার মূর্তি, পাকা হাতের কাজ—উড্রফ দেখেই বললেন, ‘এই রকম আমার একটি চাই। তুমি যে করেই হোক আমায় এই মূর্তিটি করিয়ে দাও, যত টাকা লাগে ভাবনা নেই।’ ডেকে পাঠালুম আচারী মাস্টারকে, চমৎকার কাঠের কাজ করত সে। তাকে বললুম, ‘ভালো চন্দনকাঠে তুমি এর দুটি নকল করে দাও।’ সে কয়েকদিনের মধ্যেই দুটি মূর্তি কেটে নিয়ে এল, ঠিক হুবহু সেই মূর্তিটি কপি করে ছেড়ে দিয়েছে। তার একটি উড্রফকে দিলুম, একটি আমি নিলুম। আর একটি মূর্তি, সেটি কৃষ্ণের। আধহাতমত উঁচু মূর্তিটি, বাঁশিটি ধরে আছেন মুখের কাছে; সে কি ভাব, কি ভঙ্গি, কি বলব তোমায়, মূর্তিটি দেখে আমি অবাক। অদ্ভুত মূর্তি, আইভরির রঙটি পুরানো হয়ে দেখাচ্ছে যেন পাকা সোনা। সেই মূর্তিটি দেখেই কেন জানি না আমার মনে হল, এর নিশ্চয়ই জুড়ি আছে। এমন সুন্দর কৃষ্ণের রাধা না থেকে পারে কখনো? নিশ্চয়ই এই যুগলমূর্তির পূজো হত এককালে। সেই জোড়ভাঙা রাধাকে আমার চাই। গঞ্জাম থেকে যে বন্ধু এই মূর্তিগুলি পাঠিয়েছিলেন তাঁকে লিখলুম। তিনি জানালেন, বহুকালের মূর্তিটি, অনেক খোঁজ করে পেয়েছেন, কিন্তু রাধার সন্ধান জানেন না। যাক, একজিবিশন তো হয়ে গেল। কিন্তু মনের খটকা আর যায় না, যাকে পাই খোঁজ নিই। দিল্লির দরবারেও এই মূর্তি তিনটির একজিবিশন হয়েছিল; ক্যাটালগে ছবি আছে। সবাইকে সেই ছবি দেখাই আর বলি, ‘এর রাধার সন্ধান পেলে আমায় জানাবে।’
গিরিধারী ওড়িয়া কারিগর এল সোসাইটিতে কাজ করতে। তার প্রপিতামহও খুব বড় কারিগর ছিল। তার তৈরি তিনটি কাঠের সখী আছে আমার কাছে, অতি সুন্দর। গিরিধারী বলত, তার প্রপিতামহ নাকি পুতুলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারত। সে একটা উৎসব-অনুষ্ঠানের ব্যাপার ছিল। গিরিধারীর মুখে শুনেছি, সে তখন ছোট, কাছে যাবার হুকুম ছিল না কিন্তু দেখেছে সেই উৎসবের তোড়জোড়। একবার নাকি পুরীর রাজার শখ হয়, তিনি বলেন, ‘আমি দেখতে চাই পুতুল নিজে নিজে এসে জগন্নাথকে প্রণাম করবে।’ গিরিধারীর প্রপিতামহ সেই পুতুল তৈরি করেছিলেন। পুতুল নিয়ে গেল জগন্নাথের মন্দিরের কাছে, রাজাও এলেন। কারিগর সেখানে পুতুলকে ছেড়ে দিলে, পুতুল টকটক করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে জগন্নাথকে প্রণাম করে ফিরে এল, দেখে সকলে অবাক্, রাজা বহু টাকা পুরস্কার দিলেন কারিগরকে।—সেই গিরিধারীকে বলি, যত ডিলার ছিল আমাদের নানা জায়গা থেকে আর্টিস্টিক জিনিস এনে দিত, তাদের বলি—কেউ আর হারানো রাধার সন্ধান দিতে পারে না।
মাতাপ্রসাদ নামে আমার আর-একজন লক্ষ্ণৌর ডিলার ছিল; তার কাছে যেটা চাইতুম কি রকম করে হাতে এনে দিত। তাকেও বলে রেখেছিলুম আমার ওই রাধিকা চাই। বহুদিন পর সে একদিন এল নানারকম জিনিসপত্তর নিয়ে। বসে আছি বারান্দায়; থলি থেকে একটি একটি জিনিস বের করে আমার হাতে দিচ্ছে। দেখে কোনোটা রাখব বলে পাশে রাখছি, কোনোটা ফেরত দিচ্ছি। সবশেষে সে বের করলে একটি আইভরির পুরোনো মূর্তি, লক্ষ্ণৌ থেকে এটি সে সংগ্রহ করেছে। বললে, ‘ভাঙা মূর্তি পছন্দ হবে কি না আপনার জানিনে।’ বলে সেটি আমার হাতে দিলে, মূর্তিটি হাতে নিয়ে আমার তো বুক ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। এ যে আমার সেই রাধিকা! এতদিন যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। মুখ দিয়ে আমার আর কথা সরছে না। রাধিকার যে হাতে পদ্ম ধরে আছে সেই হাতটি আছে অন্য হাতটি ভাঙা। হাত ফিরতে ফিরতে হাত ভেঙে গেছে, বা যারা পূজো করত তারাই ফেলে দিয়েছিল হাত ভেঙে যাওয়াতে, কি জানি। ডিলার যা দাম চাইলে তাকে দিয়ে ঘরে উঠে এলুম। তখনি একজন ভালো কাঠের মিস্ত্রি ডাকিয়ে আমার রাধার জন্য একহাত উঁচু একটি মন্দিরের ফরমাশ করলুম। বললুম, এমনভাবে মন্দির তৈরি করবে ভিতরে রাধাকে রেখে, আমি যেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাকে দেখতে পারি। মন্দিরের নিচে একটা চাবি থাকবে, সেটা ঘোরালেই আমার রাধা ঘুরে ফিরে দাঁড়াবে।’ সে এনে দিলে চমৎকার একটি কাঠের মন্দির তৈরি করে। তাতে রাধিকাকে প্রতিষ্ঠা করে অলকের মার হাতে দিলুম; বললুম, ‘রেখে দাও একে যত্নে তুলে। তিনি মন্দিরসুদ্ধ রাধাকে অতিযত্নে তুলে রাখলেন তার কাপড়ের আলমারিতে। মাঝে মাঝে শখ হয়, বের করে দেখি, কেউ এলে দেখাই, আবার রেখে দিই।
তার পর অনেক বছর কেটে গেছে। বহুদিন রাধাকে দেখিনি, মনেও ছিল না তেমন। সেদিন মিলাডা এসেছে। তার সঙ্গে কথায় কথায় মনে পড়ল আমার রাধিকার কথা। মিলাডা কেবল ভিনাস ভিনাস করে, ভাবলুম দিই একবার তার দর্প চূর্ণ করে। বীরুকে ডেকে বললুম, ‘আন তো বীরু আমার রাধিকাকে একবার।’ বীরু ভিতরে গিয়ে বললে পারুলকে। পারুল খুঁজে পায় না কোথা সেই মন্দিরটি। শুনে আমি নিজে গেলুম ভিতরে; বললুম, ‘সে কি কথা, রাধিকা যাবে কোথায়? আমি নিজের হাতে রেখেছি এই আলমারিতে, দেখ ভালো করে।’ মনে মনে ভয় হল, কেউ নিয়ে যায়নি তো? ভাবতেই বুকটা ধড়ফড় করে উঠল। অলকের মার অসুখ, কথা সব ভুলে যান; তাঁকে জিজ্ঞেস করি। তিনি বলেন, ‘দেখ খুঁজে, ওখানেই তো রেখেছিলুম।’ চাবি নিয়ে পারুল আলমারি খুলে তচনচ করলে; কোথাও নেই মন্দিরটি। পারুল নিচের তাক থেকে বের করলে কাঠের বাক্স থেকে একটি জাভানীজ কাঠের পুতুল। মাদাম টোন একবার এনেছিলেন জাভার নানারকম সব জিনিস, বিচিত্রা হলে তার প্রদর্শনী হয়। তার মধ্যে দুটি পুতুল ছিল; রাজকুমারী আর তার সখী। দাদা কিনলেন রাজকন্যাটি, আমি কিনলুম সখীটি। সেও ভারি সুন্দর; লাল শাড়িটি পরা, খোঁপাটি বাধা, তাতে ফুল গোঁজা। পারুল সেইটি হাতে নিয়ে বললে, ‘এইটেই কি?’ আমি বললুম, ‘আরে না। এ হল রানীর দাসী। রাধিকা হল রানী, তার কেন এমন চেহারা, এমন সাজসজ্জা হবে। খোঁজ, খোঁজ, নামাও সব কাপড়চোপড় জিনিসপত্তর আলমারি থেকে। এখানেই আছে যাবে কোথায়।’ জিনিসপত্র সব নামানো হল। না, কোথাও নেই সেই রাধিকা। হাত দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে থাকগুলি সব দেখি। কপাল দিয়ে আমার ঘাম ঝরতে লাগল। শেষে, এক কোণায় একটি বেশ বড় পার্শিয়ান কাঁচের বোল ছিল, সেইটি যেই সরিয়েছি দেখি রাধিকার মন্দির। চেঁচিয়ে উঠলুম, ‘ওরে পেয়েছি রে পেয়েছি। দেখ্ দেখ্ এই তো আমার রাধিকা ঠিক তেমনি আছে।’
অতি যত্নে রাখতে গিয়ে, আমি কি অলকের মা রেখেছিলুম ওটি কাচের বোলের পিছনে লুকিয়ে,—মনে নেই কারোই। যাক, পাওয়া তো গেল, পারুলকে বললুম, ‘এবারে জেনে রাখে ভালো করে, আর যেন না হারায়।’ তার পর এলুম বারান্দায়। যে চেয়ারে বসে পুতুল গড়তুম দেখেছ তো সেটি? তাতে হেলান দিয়ে বসে মন্দিরটি হাতে নিয়ে বললুম, ‘এবারে ডাকো মিলাডাকে।’ মিলাডা এল। বললুম, ‘কি তুমি ভিনাস ভিনাস কর। দেখ একবার, তোমাদের ভিনাস ঝক্ মেরে যাবে এর কাছে।’ ব’লে এক হাতে ধরে আর হাতে মন্দিরের দরজাটি খুলে দিলুম। মিলাডা দেখে একেবারে থ। আমি মিলাডার মুখের দিকে একবার করে তাকাই আর নিচের চাবি ঘোরাই, সঙ্গে সঙ্গে রাধিকাও ঘুরে ফিরে দাঁড়ায়। তাকে সামনে থেকে দেখালুম, পিছন থেকে দেখালুম। যে হাতে পদ্মটি ধরে আছে সেদিক থেকে দেখালুম, অন্য হাতটিও ঘোরালুম, বললুম, ‘দেখ, সব দেখ। তোমাদের ভিনাসেরও হাত নেই; কোন হাতে কি ছিল কেউ জানলও না কোনোদিন; আর আমারও রাধিকার হাত নেই। তবে এক হাতে পদ্ম আছে এটা তো জানতে পারা যাচ্ছে। এ হল আমার খণ্ডিরাধিকে। পুরীর রাজার যেমন ছিল খণ্ডিরানী, এ তেমনি আমার খণ্ডিরাধিকে।’
খণ্ডিরানীর গল্প জানো? পুরীর রাজাকে বলে চলন্ত বিষ্ণু, রাজ রথে হাত দিলে তবে রথ চলে। বহুকাল আগে একবার রথযাত্রা হবে, জগন্নাথ রথে চড়ে মাসির বাড়ি যাবেন। রাজা চলেছেন রথের আগে আগে, চামর করতে করতে। চারদিক লোকে লোকারণ্য; রথের দড়ি টানবার জন্য তীর্থযাত্রীদের তাড়াহুড়ো ঠেলাঠেলি; কেউ কেউ পড়ে যাচ্ছে ভিড়ের চাপে—দেখেছ রথযাত্রা কখনো? এখন, রথ চলেছে ভিড় ঠেলে। রাজা দেখেন পথের পাশে এক পরমাসুন্দরী ভিখারিনী ব’সে ছেঁড়া ময়লা একখানি শাড়ি পারে। রূপ দেখে রাজা গেলেন মোহিত হয়ে। বাড়ি ফিরে এসে রাজা আনালেন সেই ভিখারিনীকে; আনিয়ে রানী করলেন তাকে। সেই রানীর ছিল এক হাত কাটা, লোকে বলত তাকে খণ্ডিরানী। আমি যখন পুরীতে যাই তখনো সেই খণ্ডিরানী বেঁচে; বুড়ি হয়ে গিয়েছিল। পাশ দিয়ে যেতে পাণ্ডারা দেখাত এই খণ্ডিরানীর বাড়ি। চলন্ত বিষ্ণুর খণ্ডিরানী কালে কালে বুড়ি হয়ে গেল। কিন্তু আমার খণ্ডিরাধা? কালে কালে তার রূপ খুলছেই।
১৩. ধ্যানধারণা পুজো আর্চা
ধ্যানধারণা, পুজো আর্চা, সে আমি কোনোদিন করিনে। বড়দিকে দেখতুম, মুসোরি পাহাড়ে শার্শি বন্ধ করে বসেছেন, কুটনো বাটনা করাচ্ছেন, আর বসে বসে মালা টপকাচ্ছেন; আবার রাস্তা দিয়ে কেউ গেলে ডেকে তার খোঁজখবরও নিচ্ছেন। আমি সক্কাল বেলা উঠে বেড়িয়ে ফিরতুম। কতদিন তিনি আমায় তাড়া লাগাতেন, ‘বসে ভগবানের নাম করবে খানিক, তা নয়, কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছ সকাল থেকে?’ হেসে বলতুম, ‘ও বড়দি, এদিকে যে কত মজার মজার জিনিস সব দেখে এলুম আমি। কেমন সুন্দর পাখিটি ঝোপের ধারে বসে ছিল ঘরে বসে নাম জপলে কি দেখতে পেতুম তা?’ উলটে বড়দি মালা টপকাতে টপকাতেই আরো খানিকটা বকুনি দিয়ে চলতেন।
ধ্যানধারণা কেন করিনে জানো? একবার কি হল বলি। এখন আর ডাক্তারদের আমার লিভার ছুঁতে দিইনে। বলি, ‘ও আমার ঠিক আছে। আর যা করতে হয় কর, লিভারে হাত দিতে পারবে না।’ তা সেইবারে কোথাও কিছু না, হঠাৎ লিভারে দারুণ যন্ত্রণা। সে কি যন্ত্রণা। লিভার থেকে বুক অবধি যেন অগ্নিশূল বিঁধছে। সেই অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে শেষটায় বেঁহুশ হয়ে পড়ি। তিন-চারজন ডাক্তার চিকিৎসা করছেন। সকালের দিকে ভালো থাকি, বিকেলে ব্যথা শুরু হয়। ব্যথা শুরু হবে এই ভয়েই আমি আরো অস্থির হয়ে পড়ি বেশি। বিকেল হবার সঙ্গে সঙ্গে আমারও আতঙ্ক আরম্ভ হয়, এই বুঝি উঠল ব্যথা। যেন স্টেশনে জানান দিলে, এবারে ট্রেন আসছে বলে। একদিন সকাল থেকেই ব্যথা শুরু হয়েছে, যন্ত্রণায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছি ছেলেমাহষের মত চীৎকার করছি ‘গেলুম গেলুম।’ করুণা, নেলি, ওরা এসে জড়িয়ে ধরলে, আর বুঝি বাঁচিনে এমন অবস্থা। তিন-তিনটে মরফিয়া ইনজেকশন দিলে ডাক্তাররা; একটা সকালবেলা, একটা দুপুরে, আর একটা রাত দশটায়। ডাক্তারদের বললুম, ‘আর যা হোক একটু ঘুম পাড়িয়ে দিন আমায়, পারছিনে সইতে।’ ডাক্তাররা ভেবে মরেন, একই দিনে তিনটে মরফিয়া ইনজেকশন। তাঁরা বলেন, যে দু ডোজ মরফিয়া দেওয়া হয়েছে তাতে যে হাতিরও ঘুমিয়ে পড়বার কথা। যাই হোক আর একটাও তাঁরা দিলেন।, বললেন, ‘এতেই যা হবার হবে, আর চলবে না।’ এই বলে তারা চলে গেলেন সে-রাত্তিরের মত। আমি ঘর থেকে সবাইকে বের করে দিলুম। বললুম, ‘সবাই চলে যাও এ ঘর ছেড়ে, আমি আজ একলা থাকব।’ রাতও হয়েছিল অনেক, কদিনের উৎকণ্ঠায় ক্লান্তিতে যে যার ঘরে গিয়ে শোবামাত্রই ঘুমিয়ে পড়েছে। সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ। আমি বিছানায় শুয়ে আছি বড় বড় করে দু-চোখ মেলে—ঘুমই আসছে না তা চোখ বুজব কি? চেয়ে চেয়ে দেখছি, একটু একটু মরফিয়ার ক্রিয়া চলেছে। দেখি কি, আমার চারদিকের মশারিটা কেমন যেন কাঁপতে কাঁপতে সরে গেল,—দেয়ালও তাই। উকুনের উপর দেখ না হাওয়া গরম হয়ে কেমন কাঁপতে থাকে, দুপুরে মাঠের মাঝেও সেই রকম দেখা যায়, মরীচিকা—সেই মরীচিকার মত দেয়ালগুলো কাঁপছে চোখের সামনে। মনে হতে লাগল যেন ইচ্ছে করলেই তার ভিতর দিয়ে গলে যেতে পারি। এই হতে হতে রাত্রি প্রায় ভোর হয়ে এসেছে। চেয়েই আছি হঠাৎ দেখি, একখানি হাত, মার হাতখানি মশারির উপর থেকে নেমে এল। দেখেই চিনেছি, অসাড় হয়ে পড়ে আছি—মনে হল মা যেন বলছেন, ‘কোথায় ব্যথা? এইখানে?’ ব’লে হাতটি এসে টক করে লাগল ঠিক বুকের সেইখানটিতে। সমস্ত শরীরটা যেন চমকে উঠল, ভালো করে চারদিকে তাকালুম, কেউ কোথাও নেই। ব্যথা? নড়ে চড়ে দেখি তাও নেই। অসাড় হয়ে শুয়ে ছিলুম, নড়বার শক্তিটুকুও ছিল না একটু আগে—সেই আমি বিছানায় উঠে বসলুম। কি বলব, নিজের মনেই কেমন অবাক লাগল।
বিছানা ছেড়ে ধীরে ধীরে বাইরে এলুম, দিব্যি মানুষ, অসুখের কোনো চিহ্ন নেই। দোরগোড়ায় চাকর শুয়ে ছিল, সে ধড়মড় করে উঠে এগিয়ে এল। বললুম, ‘কাউকে ডাকিসনে। চুপচাপ একটু ঠাণ্ডা জল দে দেখিনি আমার হাতে।’ সে ঠাণ্ডা জল এনে দিলে, আমি তা ভালো করে মুখে মাথায় দিয়ে বেশ ঠাণ্ডা হয়ে চাকরকে বললুম, ‘যা এবারে আমার জন্যে এক পেয়াল চা, পুরু করে মাখন দিয়ে দুখানি পাঁউরুটি টেস্ট তৈরি করে, বাইরে বারান্দায় যেখানে বসে আমি ছবি আঁকি সেখানে এনে দে। আর দেখ্, তামাকও সেজে আনবি ভালো করে।’ চাকর নিয়ে এল। গরম গরম চা রুটি খেয়ে গড়গড়ার নলটি মুখে দিয়ে আরাম করে টানতে লাগলুম। তখন পাঁচটা বেজেছে, দাদা তেতলার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে আমায় বারান্দায় বসে থাকতে দেখে অবাক। বললেন, ‘এ কি, তুমি যে বাইরে এসে বসেছ?’ বললুম, ‘ভালো হয়ে গেছি। দাদা।’ নেলি, করুণা, অলকের মা, তার উঠে দেখে বিছানায় রুগী নেই। গেল কোথায়? এঘরে ওঘরে খোঁজাখুঁজি করে বারান্দায় এসে সকলে চেঁচামেঁচি, ‘কখন তুমি আবার বাইরে উঠে এলে, একটুও জানতে পারিনি।’ বললুম, ‘জানবে কি করে, আমি যে ভালো হয়ে গেছি একেবারে। আর তোমরা ভেবো না মিছে।’ বলতে বলতেই মহেন্দ্রবাবু ডাক্তার এসে উপস্থিত। আমায় বারান্দায় দেখেই থমকে দাঁড়ালেন। বললুম, ‘আর আপনাদের দরকার নেই।’ মহেন্দ্রবাবু হেসে বললেন, ‘ভালো কথা, সেরে উঠেছেন তা হলে? খাওয়াদাওয়া কি করলেন? বেশ বেশ, এবারে সুস্থ মানুষের মত চলাফেরা করুন। দেখুন কি রকম আপনার রোগ তাড়িয়ে দিয়েছি আমরা।’ মহেন্দ্রবাবু থাকতে থাকতেই ডাক্তার ব্রাউন উঠে এলেন খটখট করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে। আমাকে কুশলপ্রশ্ন করতেই তার হাত ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে হ্যাণ্ডশেক করে বললুম, ‘গুডবাই, ডাক্তার। আর তোমার দরকার নেই, যেতে পারো তুমি।’ সাহেব হাসিমুখে চলে গেলেন।
তাঁরা চলে যেতে মনে খটকা লাগল। ডাক্তারদের ফিরিয়ে দিলুম, বললুম, আর দরকার হবে না; কি জানি যদি আবার ব্যথা ওঠে বিকেলের দিকে। মনটা কেমন খুঁতখুঁত করতে লাগল। এমন সময়ে অমরনাথ হোমিয়োপ্যাথ ডাক্তার এসেছেন আমার খবর নিতে, তাঁকে বললুম, একটু হোমিয়োপ্যাথিই আমায় দিয়ে যাও, রেখে দিই। যদি ব্যথা ওঠে তো খাব।’ তিনি বললেন, ‘নিশ্চয়ই, আমি এখনি গিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।’ তিনি চলে যেতে এলেন বৃদ্ধ ডি. এন. রায়, তিনিও ডাক্তার, মাকে দেখতেন শুনতেন, প্রায়ই আসতেন, তিনি এসেছেন আমায় দেখতে—খবর রটে গিয়েছিল চারদিকে, আজ রাত কাটে কি না-কাটে, এমন অবস্থা। বৃদ্ধ এসেই বললেন, ‘হবে না লিভারে ব্যথা? এই বয়সে এতগুলি বই লেখা?’ ‘এতগুলি বই আবার কোথায়?’ তিনি বললেন, ‘তা নয় তো কি? বাড়ির মেয়েরা সেদিন পড়ছিল দেখলুম যে আমি।’ সে তো দুখানি মাত্র বই, শকুন্তলা আর ক্ষীরের পুতুল।’ ‘ওই হল। দুখানাই কি কম? এই বয়সে দুখানা বই লিখলে, এত এত ছবি আঁকলে, তোমার লিভার পাকবে না তো পাকবে কার?’ এতখানি বয়সে ছেলেদের জন্য দুখানি মাত্র বই লিখেছি, সেই হয়ে গেল এতগুলি বই লেখা। হেসে বাঁচিনে তাঁর কথা শুনে।
যাক সে-যাত্রা তো সেরে উঠলুম। বৃদ্ধ ডি. এন. রায়ও আমায় হোমিয়োপ্যাথি ওষুধ দিয়ে গিয়েছিলেন অনেক সাহস দিয়ে। কিন্তু সেই যে ব্যথা অদৃশ্য হল একেবারেই হল। চলে যাবার পর একটু রেশ থাকে, তাও রইল না, বুঝতেই পারতুম না যে এতখানি যন্ত্রণা পেয়েছি কয়েক ঘণ্টা আগেও। দুদিন বাদেই বেশ চলে ফিরে বেড়াতে লাগলুম, ঠিক আগের মত। তা সেইবারে ভালো হয়ে একদিন আমার মনে হল, ভগবানকে ডাকলুম না একদিনও এই এতখানি বয়সে। প্রায় তো টেঁসেই যাচ্ছিলুম এবারে। পরপারের চিন্তা তো জাগেনি মনে কখনো, ওপারে গিয়ে জবাব দিতুম কি? তাই তো, ভাবনাটা মনে কেবলই ঘোরাফেরা করতে লাগল। অলকের মাকে এসে বললুম, ‘দেখ, একটা কাঠের চৌকি চৌতলার ছাদের উপরে পাঠিয়ে দিয়ো দেখিনি চাকরদের দিয়ে। চৌকিটা ওখানেই থাকবে। কাল থেকে রোজ আমি সময়মত সেখানে নিরিবিলিতে বসে খানিকক্ষণ ভগবানের নাম করব।’ পরদিন সকালবেলা গেলুম চৌতলার ছাতে। তখনো চারদিক ফরসা হয়নি। চৌকিতে বসলুম পুবমুখো হয়ে, চোখ বুজে ডাকতে লাগলুম ভগবানকে। কি আর ডাকব, ভাবব, জানিনে তো কিছুই। মনে মনে ভগবানের একটা রূপ কল্পনা করে নিয়ে বলতে লাগলুম। ‘এতদিন তোমায় ডাকিনি, বড় ভুল হয়েছে—দয়াময় প্রভু, ক্ষমা কর আমায়।’ এমনি সব নানা ছেলেমানুষি কথা। আর চেষ্টা চলছে প্রাণে ভাব জাগিয়ে চোখে দুঁ ফোটা জল যদি আনতে পারি। এমন সময়ে মনে হল কানের কাছে কে যেন বলে উঠল, ‘চোখ বুজে কি দেখছিস, চোখ মেলে দেখ্।’ চমকে মুখ তুলে চেয়ে দেখি সামনে আকাশ লাল টকটক করছে, সূর্যোদয় হচ্ছে। সে কি রঙের বাহার, মনে হল যেন সৃষ্টিকর্তার গায়ের জ্যোতি ছড়িয়ে দিয়ে সূর্যদেব উদয় হচ্ছেন। সৃষ্টিকর্তার এই প্রভা চোখ মেলে না দেখে আমি কিনা চোখ বুজে তাকে দেখতে চেষ্টা করছিলুম। সেদিন বুঝলুম আমার রাস্তা এ নয়; চোখ বুজে তাঁকে দেখতে চাওয়া আমার ভুল। শিল্পী আমি, দুচোখ মেলে তাকে দেখে যাব জীবনভোর।
বারীন ঘোষকেও তাই বলেছিলুম। একদিন সে এল আমার কাছে,—বললে, ‘ছবি আঁকা শিখব আপনার কাছে।’ বললুম, ‘তা তো শিখবে, কিছু এঁকেছ কি? দেখাও না।’ সে একখানি দুর্গার ছবি দেখালে। বললে ‘এইটি এঁকেছি।’ দুর্গার ছবি যেমন হয় তেমনি এঁকেছে। বললুম, ‘তা দুর্গা যে এঁকেছ, কি করে আঁকলে।’ সে বললে ‘ধ্যানে বসে একটা রূপ ঠিক করে নিয়েছিলুম। পরে তাই আঁকলুম।’ আমি বললুম, ‘তা হবে না, বারীন। ধ্যানে দেখলে চলবে না, চোখ খুলে দেখতে শেখ, তবেই ছবি আঁকতে পারবে। যোগীর ধ্যান ও শিল্পীর ধ্যানে এইখানেই তফাত।’
এই আকাশে মেঘ ভেসে যাচ্ছে; কত রঙ, কত রূপ তার, কত ভাবে ভঙ্গিতে তার চলাচল। সেই যেবারে অসুখে ভুগেছিলুম, হাঁটাহাঁটি বেশি করা বারণ, বেশির ভাগ সময় বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসেই কাটিয়ে দিতুম চুপচাপ স্থির হয়ে, সামনে খোলা আকাশ, একমনে দেখতুম তা। সেই সময়ে দেখেছি কত বৈচিত্র্য আকাশের গায়ের মেঘগুলিতে। কত রূপ দেখতে পেতুম তাতে—বাড়িঘর, বনজঙ্গল, পশুপাথি, নদীপাহাড়,—যেন মানস সরোবরের রূপ ভেসে উঠত চোখের সামনে। একবার মনে হয়েছিল এই মেঘেরই এক সেট ছবি আঁকি। কত আলপনা ভেসে যাচ্ছে মেঘের গায়ে গায়ে।
সেদিন একটি ছেলেকে দেখি ডিজাইন আঁকবে, তা কাগজ সামনে নিয়ে উপরে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে আছে। বললুম, ‘ওরে, উপরে কি দেখছিস। ডিজাইন কি কড়িকাঠে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে? বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে দেখ্, কত ডিজাইনের ছড়াছড়ি সেখানে। তাও না হয়, কাগজের দিকেই চেয়ে থাক্। কড়িকাঠে কি পাবি?’ কাগজের দিকে তাকিয়ে থাকলেও অনেক সময়ে নানা জিনিস দেখা যায়। জাপানীরা তো যে কাগজে আঁকবে সেই কাগজটি সামনে নিয়ে বসে বসে দেখে; তার পর তাতে আঁকে। টাইকানকে দেখতুম, ছবি আঁকবে, পাশে রঙ কালি গুলে তুলিটি হাতের কাছে রেখে ছবি আঁকবার কাগজটির সামনে দোজানু হয়ে বসল ভোঁ হয়ে। একদৃষ্টি কাগজটি দেখল খানিক। তার পর এক সময়ে তুলিটি হাতে নিয়ে কালিতে ডুবিয়ে দু-চারটে লাইন টেনে ছেড়ে দিলে, হয়ে গেল একখানি ছবি। কাগজেই ছবিটি দেখতে পেত; দু-একটি লাইনে তা ফুটিয়ে দেবার অপেক্ষা মাত্র থাকত।
১৪. টাইকান ছিল বড় মজার মানুষ
টাইকান ছিল বড় মজার মানুষ। ওকাকুরা শেষবার যখন এসেছিলেন যাবার সময় বলে গিয়েছিলেন, ‘আমি জাপানে গিয়ে আমাদের দু-একটি আর্টিস্ট পাঠিয়ে দেব। তারা এদেশ দেখবে, নিজেরা ছবি এঁকে যাবে, তোমরা দেখতে পাবে তাদের কাজ—তাদেরও উপকার হবে তোমাদেরও কাজে লাগবে।’ তিনি ফিরে গিয়ে দুটি আর্টিস্ট পাঠালেন—টাইকানকে আর হিশিদাকে। ছেলেমানুষ তখন তারা। টাইকানের তবু একটু মুখচোখের কাঠকাঠ গড়ন ছিল, একরকম লাগত বেশ; হিশিদা ছিল একেবারে কচি, ছোট্টখাট্ট ছেলেটি। তার মুখখানি দেখলে কে বলবে যে এ ছেলে; ঠিক যেন একটি জাপানী মেয়ে, ছেলের বেশে, প্যান্টকোট-পরা; আপেলের মত লাল টুকটুক করছে দুটি গাল, কাঁচের মত কালো চোখ, মিষ্টি মুখের ভাবখানি। আমি ঠাট্টা করে তাকে বলতুম, ‘তুমি হলে মিসেস টাইকান।’ শুনে তারা দুজনেই হেসে অস্থির হত।
টাইকান আর হিশিদা সুরেনের বাড়িতেই থাকত। এদিকে ওদিকে ঘুরে ঘুরে খুব ছবি আঁকত। অনবরত স্কেচ করে যেত; কত সময়ে দেখতুম, গাড়িতে যাচ্ছি, টাইকান রাস্তার এদিকে ওদিকে তাকাতে তাকাতে বাঁ হাত বের করে তার তেলোতে ডান হাতের আঙুল বুলিয়ে চলেছে। আমি জিজ্ঞেস করতুম, ‘ও কি করছ টাইকান?’ সে বলত, ‘ফর্মটা মনে রাখছি। একবার হাতের উপরে বুলিয়ে নিলুম, লাইন মনে থাকবে বেশ।’ কখনো বা দেখতুম তাড়াতাড়ি জামার আস্তিন টেনে তাতে পেনসিল কলম দিয়ে স্কেচ করছে। নিজের সাজসজ্জার দিকে তার লক্ষ্যই ছিল না তেমন—মস্ত বড় একটা খড়ের হ্যাট মাথায় দিয়ে রোদে রোদে কলকাতার শহর বাজার ঘুরে বেড়াত, খেয়ালই করত না লোকে কি ভাববে তার ওই খ্যাপার মত সাজ দেখে। কিছু বলতে গেলে হাসত, বলত, ‘কি আর হয়েছে তাতে। জানো, এই টুপি রোদ্দুরে বেশ ঠাণ্ডা রাখে মাথা।’ টাইকান আমাদের স্টুডিয়োতে আসত, বসে কাজ করত। সেই সব ছবির আরার একজিবিশন হত, লোকে কিনত। আমরাও অনেক সময়ে ফরমাশ দিয়ে ছবি আঁকাতুম। বিদেশে এসেছে, তাদের খরচ চালাতে হবে তো— ওই ছবির টাকা দিয়েই খরচ চলত।
প্রথম যখন টাইকান ছবি আঁকলে সিল্কের উপরে হালকা কালি দিয়ে, চোখেই পড়ে না; আমাদের মোগল পার্শিয়ান ছবির কড়া রঙ দেখে দেখে অভ্যেস; আর এ দেখি, রঙ নেই, কালি, নেই, হালকা একটু ধোঁয়ার মত—এ আবার কি ধরনের ছবি। এত আশা করেছিলুম জাপানী আর্টিস্ট আসবে, তাদের কাজ দেখব, কি করে তারা ছবি আঁকে, রঙ দেয়। আর এ দেখি কোত্থেকে একটু কয়লার টুকরো কুড়িয়ে এনে তাই দিয়ে প্রথমে সিল্কে আঁকলে, তার পর পালক দিয়ে বেশ করে ঝেড়ে তার উপরে একটু হালকা কালি বুলিয়ে দিলে, হয়ে গেল ছবি। মন খারাপ হয়ে গেল। সুরেনকে বললুম, ‘ও সুরেন, ছবি যে দেখতেই পাচ্ছিনে স্পষ্ট। সুরেন বললে, ‘পাবে পাবে, দেখতে পাবে, অভ্যেস হোক আগে।’ সত্যিই তাই। কিছুদিন বাদে দেখি, দেখার অভ্যেস হয়ে গেল; তাদের ছবি ভালোও লাগতে লাগল। অনেক ছবি এঁকেছিল তারা। আমাদের দেবদেবীর ছবি আঁকবে, বর্ণনা দিতে হত শাস্ত্ৰমতে। টাইকান এঁকেছিল সরস্বতী ও কালীর ছবি দুটি; সরলার মা কিনে নিলেন।
আমাদের স্টুডিয়োর জন্যে ছবি আঁকার, দেয়ালে ছিল মস্ত বড় একটা বিলিতি অয়েল পেন্টিং—সেটা রাজেন মল্লিককে বিক্রি করে দিলুম। সেই দেয়ালের মাপে টাইকানকে বললুম ছবি এঁকে দিতে। রাসলীলা আঁকবে। বললে, ‘বর্ণনা দাও।’ বর্ণনা দিলুম। এদেশি মেয়েরা কি করে শাড়ি পরে দেখাতে হবে। বাড়ির একটি ছোট মেয়েকে ধরে এনে তাকে মডেল করে দেখালুম, এই করে শাড়ির আঁচলা ঘুরে ঘুরে যায়। শাড়ির ঘোরপেঁচ স্টাডি হল। কোথায় কি গহনা দিতে হবে পুরোনো মূর্তির ছবি ফোটো দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলুম। সব হল। এইবার সে মেঝে জুড়ে কাগজ পেতে ছবি আরম্ভ করলে। প্রথমে কয়লা দিয়ে সিল্কে ড্রইং করে তার পর একটা আসন পেতে চেপে বসল ছবির উপরে। রঙ লাগাতে লাগল একধার থেকে। দেখতে দেখতে কদিনের মধ্যেই ছবি শেষ হয়ে এল। আকাশে চাঁদের আলো ফুটল, সবই হল, কিন্তু টাইকান ছবি আর শেষ করছে না কিছুতেই। বালিগঞ্জের দিকে থাকত, সকালেই চলে আসত, এসেই ছবির উপরে ঢাকা দেওয়া কাপড়টি সরিয়ে ছবির দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে আর কেবলই এদিকে ওদিকে ঘাড় নাড়ে, কি যেন মনের মত হয়নি এখনো। রোজই দেখি এই ভাব। জিজ্ঞেস করি, ‘কোথায় তোমার আটকাচ্ছে।’ সে বলে, ‘বুঝতে পারছিনে ঠিক, তবে এইটে বুঝছি এতে একটা অভাব রয়ে গেছে।’ এই কথা বলে, ছবি দেখে, আর ঘাড় দোলায়। একদিন হল কি, এসেছে সকালবেলা, স্টুডিয়োতে ঢুকেছে—তখন শিউলি ফুল ফুটতে আরম্ভ করেছে, বাড়ির ভিতর থেকে মেয়েরা থালা ভরে শিউলি ফুল রেখে গেছেন সে-ঘরে, হাওয়াতে তারই কয়েকটা পড়েছে এখানে ওখানে ছড়িয়ে—টাইকান তাই-না দেখে ফুলগুলি একটি একটি করে কুড়িয়ে হাতে জড়ো করলে। আমি বসে বসে দেখছি তার কাণ্ড। ফুলগুলি হাতে নিয়ে ছবির উপরে ঢাকা দেওয়া কাপড়টি একটানে তুলে ছবির সামনের জমিতে হাতের সেই ফুলগুলি ছড়িয়ে দিলে, দিয়ে ভারি খুশি। থালা থেকে আরো ফুল নিয়ে ছবির সারা গায়ে আকাশে মেঘে গাছে সব জায়গায় ছড়িয়ে দিলে। এবারে টাইকানের মুখে হাসি আর ধরে না। একবার করে উঠে দাঁড়ায়, দূর থেকে ছবি দেখে, আর তাতে ফুল ছড়িয়ে দেয়, এই করে করে থালার সব কটি ফুলই ছবিতে সাজিয়ে দিলে। সে যেন এক মজার খেলা। ফুল সাজানো হলে ছবিটি অনেকক্ষণ ধরে দেখে এবারে ফুলগুলি সব আবার তুলে নিয়ে রাখলে থালাতে। শুধু একটি শিউলি ফুল নিলে বাঁ হাতে, আসন চাপালে ছবির উপরে, তার পর সাদা কমলা রং নিয়ে লাগল ছবিতে ফুলকারি করতে। একবার করে বাঁ হাতে ফুলটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আর ফুল আঁকে। দেখতে দেখতে ছবিটি ফুলে ফুলে সাদা হয়ে গেল—আকাশ থেকে যেন পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে, হাওয়াতে ফুল ভেসে এসে পড়ছে রাসলীলার নাচের মাঝে। রাধার হাতে দিলে একটি কদমফুল, গলায়ও দুলিয়ে দিলে শিউলিফুলের মালা, কৃষ্ণের বাঁশিতেও জড়ালে একগাছি। ফুলের সাদায় জ্যোৎস্না রাত্তির যেন ফুটে উঠল। এইবার টাইকান ছবি শেষ করলে, বললে, ‘এই অভাবটাই মেটাতে পারছিলুম না এতদিন।’ সেই ছবি শেষে একদিন দেয়ালে টাঙানো হল। টাইকান নিজের হাতে বাঁধাই করলে, বালুচরী শাড়ির আঁচলা লাগিয়ে দিলে ফ্রেমের চারদিকে। বন্ধুবান্ধবদের ডেকে পার্টি দেওয়া হল স্টুডিয়োতে, রাসলীলা দেখবার জন্য। বড় মজায় কেটেছে সে সব দিন।
টাইকান আমায় লাইন ড্রইং শেখাত, কি করে তুলি টানতে হয়। আমরা তাড়াতাড়ি লাইন টেনে দিই—তার কাছেই শিখলুম একটি লাইন কত ধীরে ধীরে টানে তারা। আমার কাছেও সে শিখত মোগল ছবির নানান টেকনিক। এমন একটা সৌহার্দ ছিল আমাদের মধ্যে—বিদেশী শিল্পী আর দেশী শিল্পীর মধ্যে কোনো তফাত ছিল না। এখন সেইটে বড় দেখতে পাইনে।
টাইকান দেখতুম রীতিমত নেচার স্টাডি করত—আমাদের দেশের পাতা ফুল, গাছপালা, মানুষের ভঙ্গি, গহনা, কাপড়-চোপড়, যেখানে যেটি ভালো লেগেছে খাতার পর খাতা ভরে নিয়ে গেছে। বিশেষ করে ভারতবর্ষের লোকদের মুখচোখের ছাঁদ ভারতীয় বৈশিষ্ট্য দস্তুরমত অনুশীলন করেছে। সেই সময়ে টাইকানের ছবি আঁকা দেখে দেখেই একদিন আমার মাথায় এল, জলে কাগজ ভিজিয়ে ছবি আঁকলে হয়। টাইকানকে দেখতুম ছবিতে খুব করে জলের ওয়াশ দিয়ে ভিজিয়ে নিত। আমি আমার ছবি সুদ্ধ কাগজ দিলুম জলে ডুবিয়ে। তুলে দেখি বেশ সুন্দর একটা এফেক্ট হয়েছে। সেই থেকে ওয়াশ প্রচলিত হল।
খুব কাজ করত টাইকান। হিশিদা ততটা করত না, সে বেশ এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াত। কোথায় একটু কি মাটির টুকরো পেলে, তাই ঘষে রঙ বের করলে; বাগানে সিমগাছ ছিল, ঘুরতে ঘুরতে দু-চারটে পাতা ছিঁড়ে এনে হাতে ঘষে লাগিয়ে দিলে ছবিতে। কুলগাছের ডাল পড়ে আছে কোথায়, তাই এনে একটু পুড়িয়ে কাঠকয়লার কাঠি বানিয়ে ছবি এঁকে ফেললে। বেচারা জাপানে ফিরে গিয়েই মারা গেল। মাস ছয়েক ছিল তারা এদেশে। বলেছিল আবার আসবে, আবার আর-একদল আর্টিস্ট পাঠাবে। তা আর হল না। হিশিদা বেঁচে থাকলে খুব বড় আর্টস্ট হত। একটি ছবি এঁকেছিল—দূরে সমুদ্রে আকাশে মিলে গেছে, সামনে বালুর চর, ছবিতে একটি মাত্র ঢেউ এঁকেছে যেন এসে আছড়ে পড়ছে পারে। সে যে কি সুন্দর কি বলব। পান্নার মত ঢেউয়ের রঙটি, তার গর্জন যেন কানে এসে বাজত স্পষ্ট। বড় লোভ হয়েছিল সেই ছবিটিতে। হিশিদা তো মরে গেল, টাইকান ছিল বেঁচে। খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল তাদের সঙ্গে, অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। বরাবর চিঠিপত্র লিখে খোঁজখবর রাখত।
রবিকা সেবার জাপানে যাবেন, নন্দলালকে নিয়ে গেলেন সঙ্গে, ওদের দেশে আর্টিস্টদের ভিতরে গিয়ে থেকে দেখে শুনে আসবে। নন্দলালকে বললুম, ‘টাইকানের কাছে যাবে, খালি হাতে যেতে নেই।’ আমার কাছে ছিল একটি খোদাইকরা ব্রোঞ্জ, বহু পুরোনো, নবাবদের আমলের ঘোড়ার বকলসের একটা কোনো জায়গার ডেকোরেশন হবে। সেইটি নন্দলালকে দিয়ে বললুম, ‘এইটি টাইকানকে দিয়ো আমার নাম করে। একদিকে আংটার মত আছে, বেশ ছবি টানাতে পারবে।’ আর তার স্ত্রীর জন্য দিলুম আমাদের দেশের শাড়ি ও জামার কাপড় কিছু। পরে নন্দলাল যখন ফিরে এল তার কাছে শুনি, টাইকান সেই ব্রোঞ্জটি হাতে নিয়ে মহা খুশি, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে আর হাসে।
ওকাকুরা যখন প্রথমবার আসেন এদেশে, যতদূর মনে পড়ে কলকাতায় সুরেনের বাড়িতেই ছিলেন। সেবার খুব বেশি আলাপ হয়নি তাঁর সঙ্গে। মাঝে মাঝে যেতুম, দেখতুম বসে আছেন তিনি একটা কৌচে। সামনে ব্রোঞ্জের একটি পদ্মফুল, তার ভিতরে সিগারেট গোঁজা; একটি করে তুলছেন আর ধরাচ্ছেন। বেশি কথা তিনি কখনোই বলতেন না। বেঁটেখাটাে মানুষটি, সুন্দর চেহারা, টানা চোখ, ধ্যাননিবিষ্ট গম্ভীর মূর্তি। বসে থাকতেন ঠিক যেন এক মহাপুরুষ। রাজভাব প্রকাশ পেত তার চেহারায়। সুরেনকে খুব পছন্দ করতেন ওকাকুরা। সুরেন সম্বন্ধে বলতেন, He is fit to be a king.
দ্বিতীয়বার যখন এলেন দশ বছর পরে, তখন আমি আর্টের লাইনে ঢুকেছি। প্রায়ই আমাদের জোড়াসাঁকোর স্টুডিয়োতে বসে শিল্প সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা হত। নন্দলালদের তিনি আর্টের ট্র্যাডিশন অবসার্ভেশন ও ওরিজিনালিটি বোঝাতেন তিনটি দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে। দেবতার মত ভক্তি করত ওকাকুরাকে জাপানীরা। আমাদের ছিল এক জাপানী মালী। ওকাকুরা এসেছেন শুনে দেখা করবার খুব ইচ্ছে হল তার। স্টুডিয়োতে বসে আছেন ওকাকুরা, নন্দলালের সঙ্গে কথাবার্তা কইছেন, সে এসে দরজার পাশে দূর থেকে উকিঝুঁকি দিতে লাগল। বললুম, ‘এস ভিতরে।’ কিছুতেই আর আসে না, দূরে দাঁড়িয়েই কাঁচুমাচু করে। খানিক বাদে ওকাকুরার নজরে পড়তে তিনি ডান হাতের তর্জনী তুলে ভিতরের দিকে নির্দেশ করলে পর সে হাঁটু-মুড়ে সেখান থেকেই মাথা ঝুঁকতে, ঝুঁকতে ঘরে এল। ওকাকুরাও দু-একটা কথা জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। সে আবার সেই ভাবেই হাঁটু মুড়ে বেরিয়ে গেল। যতক্ষণ ঘরে ছিল সোজা হয়ে দাঁড়ায়নি। পরে তাকে জিজ্ঞেস করলুম, ‘তুমি ওভাবে ছিলে কেন?’ সে বললে, ‘বাবা! আমাদের দেশে ওঁর কাছে যাওয়া কি সহজ কথা? আমাদের কাছে উনি যে দেবতার মত।’
সেবার ওকাকুরা ভারতবর্ষ ঘুরে ঘুরে দেখবেন। অনেক জায়গা ঘোরা হয়ে গেছে, আর দু-চার জায়গা দেখা বাকি। বললুম, যাচ্ছ যখন, কোনারকের মন্দিরটা ঘুরে দেখে এস একবার। নয় তো ভারতবর্ষের আসল জিনিসই দেখা হবে না। ওকাকুরা বললেন, ‘পুরীর মন্দিরও দেখবার বড় ইচ্ছে আমার। ব্যবস্থা করে দিতে পার?’ তখন তিনি কঠিন রোগে ভুগছেন, ভাঙা শরীর; তাই নিয়েই এসেছেন বিদেশে বিভুঁয়ে ভারতের শিল্পকীর্তি দেখতে। জগন্নাথের ডাক পড়েছে আমার বিদেশী শিল্পী ভাইকে। কিন্তু জগন্নাথ ডাকেন তো ছড়িদার ছাড়ে না; লাটবেলাটকে পর্যন্ত বাধা দেয় এত বড় ক্ষমতা সে ধরে, তাকে কিভাবে এড়ানো যায়? শিল্পীতে শিল্পীতে মন্ত্রণা বসে গেল। চুপি চুপি পরামর্শটা হল বটে, কিন্তু বন্ধু গেলেন জগবন্ধু দর্শন করতে দিনের আলোতে রাজার মত। দ্বার খুলে গেল, প্রহরী সসম্মানে একপাশ হল, জাপানের শিল্পী দেখে এলেন ভারতের শিল্পীর হাতে গড়া দেবমন্দির, বৈকুণ্ঠ, আনন্দবাজার, মায় দেবতাকে পর্যন্ত।
বড় খুশি হয়েছিলেন ওকাকুরা সেবারে কোনারক দেখে। বললেন, ‘কোনারক না দেখলে এবারকার আসাই আমার বৃথা হত। ভারতশিল্পের প্রাণের খবর মিলল আমার ওখানে।’ তাঁর বিদায়ের দিনের শেষ কথা আমার এখনও মনে আছে, ‘ধন্য হলেম, আনন্দের অবধি পেলেম, এইবার পরপারে সুখে যাত্রা করি।’ দেশে ফিরে গিয়ে কিছুকালের মধ্যেই মারা যান ওকাকুরা।
সেবারেই তিনি বলেছিলেন নন্দলালদের, ‘দশ বছর আগে যখন আমি এসেছিলাম তখন তোমাদের আজকালকার আর্ট বলে কিছুই দেখিনি। এবারে দেখছি তোমাদের আর্ট হবার দিকে যাচ্ছে। আবার যদি দশ বছর বাদে আসি তখন হয়তো দেখব হয়েছে কিছু।’
তিনিও আর এলেন না, আমিও বসে আছি দেখবার জন্যে—কই, দেখছি না তো। হয়তো আবার আমায় আসতে হবে। পথ আছে কি?
১৫. ভারতবর্ষকে যাঁরা সত্যিই ভালোবেসেছিলেন
ভারতবর্ষকে যাঁরা সত্যিই ভালোবেসেছিলেন তার মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবচেয়ে বড়। বাগবাজারের ছোট্ট ঘরটিতে তিনি থাকতেন, আমরা মাঝে মাঝে যেতুম সেখানে। নন্দলালদের কত ভালোবাসতেন, কত উৎসাহ দিতেন। অজন্তায় তো তিনিই পাঠালেন নন্দলালকে। একদিন আমায় নিবেদিতা বললেন, ‘অজন্তায় মিসেস হ্যারিংহাম এসেছে। তুমিও তোমার ছাত্রদের পাঠিয়ে দাও, তার কাজে সাহায্য করবে। দুপক্ষেরই উপকার হবে। আমি চিঠি লিখে সব ঠিক করে দিচ্ছি।’ বললুম, ‘আচ্ছা’ নিবেদিতা তখনি মিসেস হ্যারিংহামকে চিঠি লিখে দিলেন। উত্তরে মিসেস হ্যারিংহাম জানালেন, বোম্বে থেকে তিনি আর্টিস্ট পেয়েছেন তাঁর কাজে সাহায্য করবার। এরা সব নতুন আর্টিস্ট, জানেন না কাউকে, ইত্যাদি ইত্যাদি।
নিবেদিতা ছেড়ে দেবার মেয়ে নন। বুঝেছিলেন এতে করে নন্দলালদের উপকার হবে। যে করে হোক পাঠাবেনই তাদের। আবার তাঁকে চিঠি লিখলেন। আমায় বললেন, ‘খরচপত্তর সব দিয়ে এদের পাঠিয়ে দাও অজন্তায়। এ রকম সুযোগ ছেড়ে দেওয়া চলবে না।’ নিবেদিতা যখন বুঝেছেন এতে নন্দলালের ভালো হবে, আমিও তাই মেনে নিয়ে সমস্ত খরচপত্তর দিয়ে নন্দলালদের কয়েকজনকে পাঠিয়ে দিলুম অজন্তায়। পাঠিয়ে দিয়ে তখন আমার ভাবনা। কি জানি, পরের ছেলে, পাহাড়ে জঙ্গলে পাঠিয়ে দিলুম, যদি কিছু হয়। মনে আর শান্তি পাইনে, গেলুম আবার নিবেদিতার কাছে। বললুম, ‘সেখানে ওদের খাওয়াদাওয়াই বা কি হচ্ছে, রান্নার লোক নেই সঙ্গে, ছেলেমানুষ সব।’ নিবেদিতা বললেন, ‘আচ্ছা আমি সব বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।’ বলে গণেন মহারাজকে ডাকিয়ে আনলেন। ডাল চাল তেল নুন ময়দা ঘি আর একজন রাঁধুনি সঙ্গে দিয়ে বিলিব্যবস্থা বলে কয়ে গণেনকে পাঠিয়ে দিলেন নন্দলালদের কাছে। তবে নিশ্চিন্ত হই।
নিবেদিতা নইলে নন্দলালদের যাওয়া হত না অজন্তায়। কি চমৎকার মেয়ে ছিলেন তিনি। প্রথম তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় আমেরিকান কন্সলের বাড়িতে। ওকাকুরাকে রিসেপ্শন দিয়েছিল, তাতে নিবেদিতাও এসেছিলেন। গলা থেকে পা পর্যন্ত নেমে গেছে সাদা ঘাগরা, গলায় ছোট্ট ছোট্ট রুদ্রাক্ষের এক ছড়া মালা; ঠিক যেন সাদা পাথরের গড়া তপস্বিনীর মূর্তি একটি। যেমন ওকাকুরা একদিকে, তেমনি নিবেদিতা আর একদিকে। মনে হল যেন দুই কেন্দ্র থেকে দুটি তারা এসে মিলেছে। সে যে কি দেখলুম কি করে বোঝাই।
আর একবার দেখেছিলুম তাঁকে। আর্ট সোসাইটির এক পার্টি, জাস্টিস হোমউডের বাড়িতে, আমার উপরে ছিল নিমন্ত্রণ করার ভার। নিবেদিতাকেও পাঠিয়েছিলুম নিমন্ত্রণ চিঠি একটি। পার্টি শুরু হয়ে গেছে। একটু দেরি করেই এসেছিলেন তিনি। বড় বড় রাজারাজড়া সাহেব মেম গিসগিস করছে। অভিজাতবংশের বড়ঘরের মেম সব; কত তাদের সাজসজ্জার বাহার, চুল বাঁধিবারই কত কায়দা; নামকরা সুন্দরী অনেক সেখানে। তাদের সৌন্দর্যে ফ্যাশানে চারদিক ঝলমল করছে। হাসি গল্প গানে বাজনায় মাত্। সন্ধ্যে হয়ে এল, এমন সময়ে নিবেদিতা এলেন। সেই সাদা সাজ, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথার চুল ঠিক সোনালি নয়, সোনালি রুপোলিতে মেশানো, উঁচু করে বাঁধা। তিনি যখন এসে দাঁড়ালেন সেখানে, কি বলব যেন নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে চন্দ্রোদয় হল। সুন্দরী মেমরা তাঁর কাছে যেন এক নিমেষে প্রভাহীন হয়ে গেল। সাহেররা কানাকানি করতে লাগল। উড্রফ, ব্লান্ট এসে বললেন, ‘কে এ?’ তাদের সঙ্গে নিবেদিতার আলাপ করিয়ে দিলুম।
‘সুন্দরী সুন্দরী’ কাকে বল তোমরা জানিনে। আমার কাছে সুন্দরীর সেই একটা আদর্শ হয়ে আছে। কাদম্বরীর মহাশ্বেতার বর্ণনা—সেই চন্দ্রমণি দিয়ে গড়া মূর্তি যেন মূর্তিমতী হয়ে উঠল।
নিবেদিতা মারা যাবার পর একটি ফোটো গণেন মহারাজকে দিয়ে জোগাড় করেছিলুম, আমার টেবিলের উপর থাকত সেখানি। লর্ড কারমাইকেল, তাঁর মত আর্টিস্টিক নজর বড় কারো ছিল না। আমাদের নজরে নজরে মিল ছিল। আর্টেরই শখ তাঁর। জার্মান-যুদ্ধের ঠিক আগে জাহাজ-বোঝাই তাঁর যা কিছু ভালো ভালো জিনিস ও আমাদের আঁকা একপ্রস্থ ছবি বিলেতে পাঠিয়েছিলেন। সেই জাহাজ গেল ডুবে ভূমধ্যসাগরে। তিনি দুঃখ করেছিলেন, ‘আমার আসবাবপত্র সব যায় যাক কোনো দুঃখ নেই, কিন্তু তোমাদের ছবিগুলো যে গেল এইটেই বড় দুঃখের কথা।’ নন্দলাল যখন এসে দুঃখ করলে তাকে স্তোকবাক্য দিয়েছিলুম, ‘ভালোই হয়েছে, এতে দুঃখ কি। আমি দেখছি জলদেবীরা আমাদের ছবিগুলো বরুণালয়ে টাঙিয়ে আনন্দ করছেন। গেছে যাক, ভেবো না।’ সেই লর্ড কারমাইকেল একদিন আমার টেবিলের উপর নিবেদিতার ফোটােখানি দেখে ঝুঁকে পড়লেন, বললেন, ‘এ কার ছবি?’ বললুম, ‘সিস্টার নিবেদিতার।’ তিনি বললেন, ‘এ-ই সিস্টার নিবেদিতা? আমার একখানি এইরকম ছবি চাই।’ বলেই আর বলাকওয়া না, সেই ছবিখানি বগলদাবা করে চলে গেলেন। ছবিখানি থাকলে বুঝতে পারতে সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা কাকে বলে। সাজগোজ ছিল না, পাহাড়ের উপর চাঁদের আলো পড়লে যেমন হয় তেমনি ধীর স্থির মূর্তি তাঁর। তাঁর কাছে গিয়ে কথা কইলে মনে বল পাওয়া যেত।
বিবেকানন্দকেও দেখেছি। কর্তাদাদামশায়ের কাছে আসতেন। দীপুদার সহপাঠী ছিলেন; ‘কি হে নরেন’ বলে তিনি কথা বলতেন। বিবেকানন্দের বক্তৃতা শোনবার ভাগ্য হয়নি আমার, তার চেহারা দেখেছি; কিন্তু আমার মনে হয় নিবেদিতার কাছে লাগে না। নিবেদিতার কি একটা মহিমা ছিল; কি করে বোঝাই সে কেমন চেহারা। দুটি যে দেখিনে আর, উপমা দেব কি।
শিল্পের পথে চলতে চলতে ভালো মন্দ জ্ঞানী মূর্খ অনেকের সংস্পর্শেই এসেছি। সইতে হয়েছে অনেক কিছু। বলি এক ঘটনা।
লাটবন্ধুও আসত যেমন, রাজবন্ধুও আসত অনেক। রবিকা জাপান থেকে ‘অন্ধ ভিখিরী’ ছবি আনলেন; নামকরা শিল্পীর আকা, মস্ত সিল্কে। কি ছবির কারুকাজ, প্রতিটি চুলের কি টান, দেখলে অবাক হয়ে যেতে হয়। বিচিত্রা হলে টানানো হল সেই ছবি। এখন এক রাজবন্ধু এসেছেন দেখতে; শিল্পের সমজদার বলে নাম আছে তাঁর। আমার দুর্বুদ্ধি, তাঁকে বোঝাতে গেছি জাপানী শিল্পীর তুলির টানের বাহাদুরি, কি করে একটি টানে একটি চুল এঁকেছে। রাজবন্ধু চোখ বুজে ভাবলেন খানিক, ভেবে বললেন ‘অবনিবাবু, আমি দেখেছি গাড়ির চাকায় যার লাইন টানে তারাও এর চেয়ে সূক্ষ্ম লাইন টানে।’ শুনে আমার একেবারে বাক্রোধ। এমন ধাক্কা আমি কখনো খাইনি। দেখেছি ইউরোপীয়ানরা ঢের বেশি ছবি বুঝত, রস পেত, দু-এক কথাতেই বোঝা যেত তা।
রাজবন্ধু তো ওই কথা বললেন, অথচ দেখ একটা সামান্য লোকের কথা। ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির একজিবিশন হচ্ছে কর্পোরেশন স্ট্রীটের একতলা ঘরে। ভালো ভালো ছবি সব টাঙানো হয়েছে—লাটবেলাট, সাহেবসুবো, বাবুভায়া, কেরানী, ছাত্র, মাস্টার পণ্ডিত সব ঘুরে ঘুরে দেখছেন। আমিও ঘুরছি বন্ধুদের সঙ্গে। কয়েকটি পাঞ্জাবী ট্যাক্সিড্রাইভার রাস্তা থেকে উঠে এসে ঘুরে ঘুরে ছবি দেখতে লাগল। আমাদের ড্রাইভারটাও ছিল সেই সঙ্গে। কৌতুহল হল, দেখি, এরা ছবি সম্বন্ধে কি মন্তব্য করে। জিজ্ঞেস করলুম, ‘কি, কিরকম লাগছে?’ একটি ড্রাইভার একখানি খুব ভালো ছবিই দেখিয়ে বললে, এই ছবিখানি যেমন হয়েছে আর কোনোটা তেমন হয়নি। সেটা কার ছবি এখন মনে নেই। সেদিন বুঝলুম এরাও তো ছবি বোঝে। তার কারণ সহজ চোখে ছবি দেখতে শিখেছে এর।
ওইরকম মতিবুড়ো একবার বলেছিলেন আমায়, ‘ছোটবাবু, একটা কথা বলব, রাগ করবেন না?’
বললুম, ‘না রাগ কেন করব, বলুন না?’
‘দেখুন, ছোটবাবু, আপনার ছাত্র নন্দলাল, সুরেন গাঙুলী, ওরা ছবি আঁকে, দেখে মনে হয় বেশ যত্ন করে ভালো ছবিই এঁকেছে। কিন্তু আপনার ছবি দেখে তো তা মনে হয় না।’
‘ছবি বলে মনে হয় তো?’
‘তাও নয়।’
‘তবে কি মনে হয়?
‘মনে হয়—’
‘বলেই ফেলুন না, ভয় কি?’
‘আপনার ছবি দেখলে মনে হয় আঁকা হয়নি মোটেই।’
‘সে কি কথা! আপনার কাছে বসেই আঁকি আমি, আর বলছেন আঁকা বলেই মনে হয় না।’
‘না, মনে হয় যেন ওই কাগজের উপরেই ছিল ছবি।’
বড় শক্ত কথা বলেছিলেন তিনি। শক্ত সমালোচক ছিলেন বুড়ো, বড় সার্টিফিটেই দিয়েছিলেন আমায়। একথা ঠিক, এঁকেছি চেষ্টা করেছি, এ সমস্ত ঢাকা দেওয়াই হচ্ছে ছবির পাকা কথা। গান সম্বন্ধেও এই কথাই শাস্ত্রে বলেছে। আকাশের পাখি যখন উড়ে যায়, বাতাসে কোনো গতাগতির চিহ্ন রেখে যায় না। সুরের বেলা যেমন এই কথা, ছবির বেলাও সেই একই কথা।
১৬. সকাল থেকে ঝির ঝির করে বৃষ্টি
সকাল থেকে ঝির ঝির করে বৃষ্টি পড়ছে। বসে থাকতে থাকতে মনে হল গঙ্গার রূপ—বর্ষায় গঙ্গা হয়তো ভরে উঠেছে এতক্ষণে।
সেবার এখান থেকে কলকাতায় গিয়ে একবার গেলুম দক্ষিণেশ্বরে গঙ্গাকে দেখতে। কিন্তু সে গঙ্গাকে যেন পেলেম না আর কোথাও। কোথায় গেল তার সেই রূপ। মনে হল কে যেন গঙ্গার আঁচল কেটে সেখানে বিচ্ছিরি একটা ছিটের কাপড় জুড়ে দিয়েছে। চারদিকে খানিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ফিরে এলেম বাড়িতে। কিন্তু দেখেছি আমি গঙ্গার সেই রূপ।—
‘বন্দ্য মাতা সুরধুনী পুরাণে মহিমা শুনি পতিত পাবনী পুরাতনী।’
শিশুবোধ পড়তুম, বড় চমৎকার বই, অমন বই আমি আর দেখিনে। এখনকার ছেলেরা পড়ে না সে বই—
কুরুবা কুরুবা কুরুবা লিজ্জে
কাঠায় কুরুবা কুরুবা লিজ্জে
কাঠায় কাঠায় ধুল পরিমাণ
দশ বিশ কাঠায় কাঠায় জান।
আমার যাত্রায় ছাগলের মুখে এই গান জুড়ে দিয়েছিলুম। কেমন সুন্দর কথা বল দেখিনি, যেন কুর কুর করে ঘাস খাচ্ছে ছাগলছানা।
আরো সব নানা গল্প ছিল, দাতা কর্ণের গল্প, প্রহ্লাদের গল্প, সন্দীপনী মুনির পাঠশালায় কেষ্ট বলরাম পড়তে যাচ্ছেন, সন্দীপনী মুনির দ্বারে কেষ্ট বলরাম, আরো কত কি। বড় হয়েও এই সেদিনও পড়েছি আমি বইখানি মোহনলালকে দিয়ে আনিয়ে।
তা সেই সুরধনী গঙ্গাকে দেখেছি আমি। ছেলেবেলায় কোন্নগরের বাগানে বসে বসে দেখতুম—দুকূল ছাপিয়ে গঙ্গা ভরে উঠেছে, কুলু কুলু ধ্বনিতে বয়ে চলেছে; সে ধ্বনি সত্যিই শুনতে পেতুম। ঘাটের কাছে বসে আছি, কানে শুনছি তার সুর, কুল্ কুল্ ঝুপ্, কুল্ কুল্ ঝুপ্—আর চোখে দেখছি তার শোভা—সে কী শোভা, সেই ভরা গঙ্গার বুকে ভরা পালে চলেছে জেলে নৌকো, ডিঙি নৌকো। রাত্তিরবেলা সারি সারি নৌকোর নানারকম আলো পড়েছে জলে। জলের আলো ঝিলমিল করতে করতে নৌকোর আলোর সঙ্গে সঙ্গে নেচে চলত। কোনো নৌকোয় নাচগান হচ্ছে, কোনো নৌকোয় রান্নার কালে হাঁড়ি চেপেছে, দূর থেকে দেখা যেত আগুনের শিখা।
স্নানযাত্রীদের নৌকো সব চলেছে পর পর। রাতের অন্ধকারে সেও আর এক শোভা গঙ্গার। গঙ্গার সঙ্গে অতি নিকট সম্বন্ধ তেমন ছিল না; চাকররা মাঝে মাঝে গঙ্গাতে স্নান করাতে নিয়ে যেত, ভালো লাগত না, তাদের হাত ধরেই দু-বার জলে ওঠানামা করে ডাঙার জীব ডাঙায় উঠে পালিয়ে বাঁচতুম। কিন্তু দেখেছি, এমন দেখেছি যে দেখার ভিতর দিয়েই গঙ্গাকে অতি কাছে পেয়েছি।
তার পর বড় হয়ে আর একবার গঙ্গাকে আর এক মূর্তিতে দেখি। খুব অসুখ থেকে ভুগে উঠেছি নিজে ওঠবার বসবার ক্ষমতা নেই। ভোর ছটায় তখন ফেরি স্টীমার ছাড়ে, জগন্নাথ ঘাট থেকে শিবতলা ঘাট হয়ে ফেরে নটা সাড়ে নটায়। বিকেলেও যায়, আপিসের বাবুদের পৌঁছে দিয়ে আসে। ঘণ্টা দুই-আড়াই লাগে। ডাক্তার বললেন, গঙ্গার হাওয়া খেলে সেরে উঠব তাড়াতাড়ি। নির্মল আমায় ধরে ধরে এনে বসিয়ে দিলে স্টীমারের ডেকে একটা চেয়ারে। মনে হল যেন গঙ্গাযাত্রা করতে চলেছি। এমনি তখন অবস্থা আমার। কিন্তু সাত দিন যেতে না-যেতে গঙ্গার হাওয়ায় এমন সেরে উঠলুম, নির্মলকে বললুম, ‘আর তোমায় আসতে হবে না, আমি একাই যাওয়া-আসা করতে পারব।’
সেই দেখেছি সেবারে গঙ্গার রূপ। গ্রীষ্ম বর্ষ শরৎ হেমন্ত শীত বসন্ত কোনো ঋতুই বাদ দিইনি, সব ঋতুতেই মা গঙ্গাকে দেখেছি। এই বর্ষাকালে দুকূল ছাপিয়ে জল উঠেছে গঙ্গার,—লাল টকটক করছে। জলের রং—তোমরা খোয়াইধোয়া জলের কথা বল ঠিক তেমনি, তার উপরে গোলাপী পাল তোলা ইলিশ মাছের নৌকো এদিকে ওদিকে দুলে দুলে বেড়াচ্ছে, সে কি সুন্দর। তার পর শীতকালে বসে আছি ডেকে গরম চাদর গায়ে জড়িয়ে, উত্তুরে হাওয়া মুখের উপর দিয়ে কানের পাশ ঘেঁষে বয়ে চলেছে হু হু করে। সামনে ঘন কুয়াশা, তাই ভেদ করে স্টীমার চলেছে একটানা। সামনে কিছুই দেখা যায় না। মনে হত যেন পুরাকালের ভিতর দিয়ে নতুন যুগ চলেছে কোন রহস্য উদ্ঘাটন করতে। থেকে থেকে হঠাৎ একটি দুটি নৌকো সেই ঘন কুয়াশার ভিতর থেকে স্বপ্নের মত বেরিয়ে আসত।
দেখেছি, গঙ্গার অনেক রূপই দেখেছি। তাই তো বলি, আজকাল ভারতীয় শিল্পী বলে নিজেকে যারা পরিচয় দেয় ভারতীয় তারা কোন্খানটায়? ভারতের আসল রূপটি তারা ধরল কই? তাদের শিল্পে ভারত স্থান পায়নি মোটেই। কারণ তারা ভারতকে দেখতে শেখেনি, দেখেনি। এ আমি অতি জোরের সঙ্গেই বলছি। আমি দেখেছি, নানারূপে মা গঙ্গাকে দেখেছি। তাই তো ব্যথা বাজে, যখন দেখি কি জিনিস এরা হারায়। কত ভালো লাগত, কত আনন্দ পেয়েছি গঙ্গার বুকে। একদিনও বাদ দিইনি, আরো দেখবার, ভালো করে দেখবার এত প্রবল ইচ্ছে থাকত প্রাণে। গঙ্গার উপরে সে বয়সে কত হৈচৈই না করতুম। সঙ্গী সাথিও জুটে গেল। গাইয়ে বাজিয়েও ছিল তাতে। ভাবলুম, এ তে মন্দ নয়। গানবাজনা করতে করতে আমাদের গঙ্গা-ভ্রমণ জমবে ভালো। যেই না ভাবা, পরদিন বাঁয়া তবলা হারমোনিয়ম নিয়ে তৈরি হয়ে উঠলুম স্টীমারে। বেশির ভাগ স্টীমারে যারা বেড়াতে যেত তারা ছিল রুগীর দল। ডাক্তারের প্রেসকিপশন গঙ্গার হাওয়া খেতে হবে, কোনোরকমে এসে বসে থাকেন— স্টীমার ঘণ্টা কয়েক চলে ফিরে ঘুরে এসে লাগে ঘাটে, গঙ্গার হাওয়া খেয়ে তারাও ফিরে যায় যে যার বাড়িতে। আর থাকত আপিসের কেরানিবাবুরা, কলকাতার আশপাশ থেকে এসে আপিস করে ফিরে যায় রোজ। সেই একঘেয়েমির মধ্যে আমরা দু-চারজন জুড়ে দিলুম গানবাজনা। কি উৎসাহ আমাদের, দু-দিনেই জমে উঠল খুব। রায়বাহাদুর বৈকুণ্ঠ বোস মশায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক, তিনিও আসেন স্টীমারে বেড়াতে। সম্প্রতি অসুখ থেকে উঠেছেন, খুব ভাল বাঁয়া তবলা বাজাতে পারতেন এককালে, তিনিও জুটে পড়লেন আমাদের দলে বাঁয়া তবলা নিয়ে। কানে একদম শুনতে পেতেন না, কিন্তু কি চমৎকার তবলা বাজাতেন। বললুম, ‘কি করে পারেন?’ তিনি বললেন, ‘গাইয়ের মুখ দেখেই বুঝে নিই।’ গানও হত, নিধুবাবুর টপ্পা, গোপাল উড়ের যাত্রা, এই সব। গানবাজনায় হৈ হৈ করতে করতে চলেছি—এদিকে গঙ্গাও দেখছি। এ খেয়ায় ও খেয়ায় স্টীমার থেমে লোক তুলে নিচ্ছে, ফেরি বোটও চলেছে যাত্রী নিয়ে। মাঝে মাঝে গঙ্গার চর—সে চরও আজকাল আর দেখিনে। ঘুষুড়ির চড়া বরাবর দেখেছি, বাবামশায়দের আমলেও তাঁরা যখন পলতার বাগানে যেতেন, ওই চরে থেমে স্নান করে রান্নাবান্নাও হত কখনো কখনো চরে, সেখানেই খাওয়াদাওয়া সেরে আবার বোট ছেড়ে দিতেন। বরাবরের এই ব্যবস্থা ছিল। এবারে ছেলেদের জিজ্ঞেস করলুম, ‘ওরে সেই চর কোথায় গেল? দেখছিনে যে। গঙ্গার কি সবই বদলে গেল? এ যে সেই গঙ্গা বলে আর চেনাই দায়।’
তা সেই তখন একদিন দেখলুম। সে যে কি ভালো লেগেছিল। স্টীমার চলেছে খেয়া থেকে যাত্রী তুলে নিয়ে। সামনে চর যেন—এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর তার মাঝে বসে আছে শিবু সদাগর। ওপাশের ঘাটে একটি ডিঙি নৌকো। ছোট্ট গ্রামের ছায়া পড়েছে, ঘাটে ডিঙি নৌকায় ছোট্ট একটি বউ লাল চেলি পরে বসে—শ্বশুরবাড়ি যাবে, কাঁদছে চোখে লাল আঁচলটি দিয়ে, পাশে বুড়ি দাই গায়ে হাত বুলিয়ে সান্তত্বনা দিচ্ছে, নদীর এপার বাপের বাড়ি, ওপার শ্বশুরবাড়ি—ছোট্ট বউ কেঁদেই সারা ওইটুকু রাস্তা পেরতে। সে যে কি সুন্দর দৃশ্য, কি বলব তোমায়। মনের ভিতর আঁকা হয়ে রইল সেদিনের সেই ছবি, আজও আছে ঠিক তেমনটিই। এমনি কত ছবি দেখেছি তখন। গঙ্গার দুদিকে কত বাড়ি ঘর, মিল, ভাঙা ঘাট, কোথাও বা দ্বাদশ মন্দির, চৈতন্যের ঘাট, বটগাছটি গঙ্গার ধারে ঝুঁকে পড়েছে তারই নিচে এসে বসেছিলেন চৈতন্যদেব—গদাধরের পাট, এই সব পেরিয়ে স্টীমার চলত এগিয়ে। গান হৈ-হল্লার ফাঁকে ফাঁকে দেখাও চলত সমানে। এই দেখার জন্য ছেলেবেলার এক বন্ধুকে কেমন একদিন তাড়া লাগিয়েছিলুম। বলাই, ছেলেবেলায় এক সঙ্গে পড়েছি—অসুখে ভোগার পর একদিন দেখি সেও এসেছে স্টীমারে, দেখে খুব খুশি। খানিক কথাবার্তার পর সে পকেট থেকে একটি বই বের করে পাতা খুলে চোখের সামনে ধরলে, দেখি একখানি গীতা। একমনে পড়েই চলল, চোখ আর তোলে না পুথির পাতা থেকে। বললে, ‘মা বলে দিয়েছেন গীতা পড়তে, আমায় বিরক্ত কোরো না।’ বললুম, ‘বলাই, ও বলাই, বইটা রাখ্ না। কি হবে ও-বই পড়ে, চেয়ে দেখ্ দেখিনি কেমন দুপাতা খোলা রয়েছে সামনে, আকাশ আর জল, এতেই তোর গীতার সব কিছু পাবি। দেখ্ না একবারটি চেয়ে দেখ ভাই।’ বলাই মুখ তোলে না। মহামুশকিল।
ধম্মকম্ম আমার সয় না। কোনোকালে করিওনি। ওসব দিকই মাড়াইনে। আর তা ছাড়া প্রথম প্রথম যখন আসি স্টীমারে, একদিন পিছনে সেকেণ্ড ক্লাসে বসে কেরানিবাবুরা এ ওর গায়ে ঠেলা মেরে চোখ ইশারা করে বলছে, ‘কে রে, এ কে এল?’ একজন বললে, ‘অবন ঠাকুর ঠাকুরবাড়ির ছেলে।’ আর একজন বললে, ‘ও, তাই, বয়েসকালে অনেক অত্যাচার করেছে এখন এসেছে পরকালের কথা ভেবে গঙ্গায় পুণ্যি করতে।’ শুনেছিলুম আপন মনেই। কিন্তু কথাটা মনে ছিল।
অবিনাশ ছিল আমাদের মধ্যে ষণ্ডাগুণ্ডা ধরনের। আমার সঙ্গে আসত গানবাজনার আড্ডা জমাতে। তাকে ঠেলা দিয়ে বললুম, ‘দেখ না অবিনাশ, ওদিকে যে গীতার পাতা থেকে চোখই তুলছে না বলাই আর কোনোদিকে।’ শুনে অবিনাশ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে, বলাই বই পড়ছে ঘাড় গুঁজে তার ঘাড়ের কাছে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে বইটি ছোঁ মেরে নিয়ে একেবারে তার পকেটজাত করলে। বলাই চেচিয়ে উঠল, ‘কর কি, কর কি মা বলে দিয়েছেন সকাল-বিকেল গীতা পড়তে।’ আর গীতা! অবিনাশ বললে, ‘বেশি বাড়াবাড়ি কর তো গীতা জলে ফেলে দেব।’ বলাই আর কি করে, সেও শেষে আমাদের গানে বাজনায় যোগ দিলে। কেরানিবাবুরা দেখি উৎসুক হয়ে থাকেন আমাদের গানবাজনার জন্য। যে কেরানিবাবু আমাকে ঠেস দিয়ে সেদিন ওই কথা বলেছিলেন তিনি একদিন স্টীমারে উঠতে গিয়ে পা ফসকে গেলেন জলে পড়ে, আমরা তাড়াতাড়ি সারেঙকে বলে তাকে টেনে তুলি জল থেকে। পরে আমার সঙ্গে তাঁর খুব ভাব হয়ে যায়। তখন যে কেউ আসত আমাদের ওই দলে যোগ না দিয়ে পারত না। একবার এক যাকে বলে ঘোরতর বুড়ো—নাম বলব না—শরীর সারাতে স্টীমারে এসে হাজির হলেন। দেখে তো আমার মুখ শুকিয়ে গেল। অবিনাশকে বললুম, ‘ওহে অবিনাশ, এবারে বুঝি আমাদের গান বন্ধ করে দিতে হয়। টপ্পা খেয়াল তো চলবে না আর ধর্ম-সংগীত ছাড়া।’ সবাই ভাবছি বসে, তাই তো। আমাদের হারমোনিয়ম দেখে তিনি বললেন, ‘তোমাদের গানবাজনা হয় বুঝি। তা চলুক না, চলুক।’ মাথা চুলকে বললুম, ‘সে অন্য ধরনের গান।’ তিনি বললেন, বেশ তো তাই চলুক, চলুক না। ভয়ে ভয়ে গান আরম্ভ হল। দেখি তিনি বেশ খুশি মেজাজেই গান শুনছেন। তাঁর উৎসাহ দেখে আর আমাদের পায় কে—দেখতে দেখতে টপাটপ টপ্পা জমে উঠল। শুধু গানই নয়, নানারকম হৈচৈও করতুম, সমস্ত স্টীমারটি সারেঙ থেকে মাঝিরা অবধি তাতে যোগ দিত। জেলে নৌকো ডেকে ডেকে মাছ কেনা হত—ইলিশ মাছ, তপসে মাছ। একদিন ভাই রাখালি অনেকগুলি তপসে মাছ কিনে বাড়ি নিয়ে গেল। পরদিন জিজ্ঞেস করলুম, ‘কি ভাই কেমন খেলি তপসে মাছ?’ সে বললে, ‘আর বোলো না দাদা, আমায় আচ্ছা ঠকিয়ে দিয়েছে। তপসে নয়, সব ভোলামাছ দিয়ে দিয়েছিল, ভোলামাছ দিয়ে ভুলিয়ে ঠকিয়ে দিলে।’ আমরা সব হেসে বাঁচিনে। সেই রাখালি বলত, ‘অবনদাদা, তুমি যা করলে, দিল্লিতে মেডেল পেলে, খেতাব পেলে, ছবি এঁকে হিস্ট্রিতে তোমার নাম উঠে গেল।’ এতেই ভায়া আমার খুশি। আমাদের স্টীমারযাত্রীদের সেই দলটির নাম দিয়েছিলুম গঙ্গাযাত্রী ক্লাব। এই গঙ্গাযাত্রী ক্লাবের জন্য স্টীমার কোম্পানির আয় পর্যন্ত বেড়ে গিয়েছিল। দস্তুরমত একটি বিরাট আড্ডা হয়ে উঠেছিল। একবার ডারবির লটারির টিকিট কেনা হল ক্লাবের নামে। সকলে এক টাকা করে চাঁদা দিলুম। টাকা পেলে ক্লাবের সবাই সমান ভাগে ভাগ করে নেব। বৈকুণ্ঠবাবু প্রবীণ ব্যক্তি, তাকেই দেওয়া হল টাকাটা তুলে। তিনি ঠিকমত টিকিট কিনে যা যা করবার সব ব্যবস্থা করলেন। ওদিকে রোজই একবার করে সবাই জিজ্ঞেস করি, ‘বৈকুণ্ঠবাবু, টিকিট কিনেছেন তো ঠিক?’ তিনি বলেন, ‘হ্যাঁ, সব ঠিক আছে, ভেবো না। টাকাটা পেলে ঠিকমতই ভাগাভাগি হবে।’ তা তো হবে, কিন্তু মুখে মুখে কথা সব, লেখাপড়া তো হয়নি কিছুই। অবিনাশকে বললুম, ‘অবিনাশ, এই তো ব্যাপার, কি হবে বল তো?’ অবিনাশ ছিল ঠোঁটকাটা লোক, পরদিন বৈকুণ্ঠবাবু স্টীমারে আসতেই সে চেপে ধরলে, ‘বৈকুণ্ঠবাবু, আপনাকে উইল করতে হবে।’ ‘উইল? সে কি, কেন?’ ‘কেন নয়, আপনাকে করতেই হবে।’ বৈকুণ্ঠবাবু দারুণ ঘাবড়ে গেলেন—বুঝতে পারছেন না কিসের উইল। অবিনাশ বললে, ‘টাকাটা পেলে শেষে যদি আপনি আমাদের না দেন বা মরে-টরে যান, টিকিট তো আপনার কাছে। তখন কি হবে? আজই আপনাকে উইল করতে হবে।’ বৈকুণ্ঠবাবু হেসে বললেন, ‘এই কথা? তা বেশ তো, কাগজ কলম আনো।’ তখনি কাগজ কলম জোগাড় করে বসল সবাই গোল হয়ে। কি ভাবে লেখা যায়, উকিল চাই যে উকিল ছিলেন একজন সেখানে—তিনিও গঙ্গাযাত্রী ক্লাবের মেম্বার, ডিসপেপসিয়ায় ভুগে ভুগে কঙ্কালসার দেহ হয়েছে তাঁর। তাঁকেই চেপে ধরা গেল, তিনি মুসাবিদা করলেন—উইল তৈরি হল, গঙ্গাযাত্রী ক্লাবের টিকিটে যে টাকা পাওয়া যাবে তা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সমান ভাগে পাবে ও আমার অবর্তমানে আমার ভাগ আমার সহধর্মিণী শ্ৰীমতী অমুক পাবেন ব’লে নিচে বৈকুণ্ঠবাবু নাম সই করলেন। উইল তৈরি। কিছুদিন বাদে ডারবির খেলা শুরু হল। রোজই কাগজ দেখি আর বলি, ‘ও বৈকুণ্ঠবাবু, ঘোড়া উঠল?’ জানি যে কিছুই হবে না তবু রোজই সকলের ওই এক প্রশ্ন। একদিন এইরকম ‘ও বৈকুণ্ঠবাবু, ঘোড়া উঠল’ প্রশ্ন করতেই বৈকুণ্ঠবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, ‘ঘোড়া উঠেছে, ঘোড়া উঠেছে, ওই দেখুন, সামনে।’ চেয়ে দেখি বরানগরের পরামানিক ঘাটের কাছ বরাবর একজোড়া কালো ঘোড়৷ জল থেকে উঠছে। স্নান করাতে জলে নামিয়েছিল তাদের। অমনি রব উঠে গেল, আমাদের ঘোড়া উঠেছে, ঘোড়া উঠেছে। গঙ্গাযাত্রীদের কপালে ঘোড়া ওই জল থেকেই উঠে রইল শেষ পর্যন্ত।
কি দুরন্তপনা করেছি তখন মা গঙ্গার বুকে। কত রকমের লোক দেখেছি, কতরকম ক্যারেক্টার সব। একদিন এক সাহেব এসে ঢুকল স্টীমারে। গঙ্গাপারের কোন্ মিলের সাহেব, লম্বাচওড়া জোয়ান ছোকরা, হাতে টেনিস ব্যাট, দেখেই মনে হয় সদ্য এসেছে বিলেত থেকে। সাহেব দেখেই তো আমরা যে যার পা ছড়িয়ে গম্ভীর ভাবে বসলুম সবাই, মুখে চুরুট ধরিয়ে। সাহেব ঢুকে এদিক ওদিক তাকাতেই সেই ডিস্পেপটিক উকিল তাড়াতাড়ি তাঁর জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। সাহেব বসে পড়ল সেখানে। আড়ে আড়ে দেখলুম, এমন রাগ হল সেই উকিলের উপর। সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের চাপরাসিও এসে জায়গার জন্য ঠেলাঠেলি করতে লাগল ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট হাতে নিয়ে—টিকিট আছে তো এখানে সে বসবে না কেন? অবিনাশ তো উঠল রুখে, বললে, ‘ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট আছে তো নিচে যা, সেখানে কেবিনে বোস গিয়ে—এখানে আমাদের সমান হয়ে বসবি কি?’ বলে জামার হাতা গুটোতে লাগল। দেখি একটা গোলযোগ বাধবার জোগাড়। গোলযোগ শুনে সাহেবও উঠে দাঁড়িয়েছে, বুঝতে পারছে না কিছু। সাহেবকে বললুম, ‘চাপরাসিকে এখানে ঢুকিয়েছ কেন, তাকে পিছনে যেতে বল।’ বিলিতি সাহেব, এদেশের হালচাল জানে না, ব্যাপারটা বুঝে চাপরাসিকে পিছনে পাঠিয়ে দিলে। সাহেবটি লোক ছিল ভালো। খানিক বাদে সে নেমে গেল চাপরাসিকে নিয়ে। উকিলকে বললুম, ‘সাহেব তোমায় কি জিজ্ঞেস করছিল হে?’ সে বললে, ‘সাহেব জানতে চাইলে তুমি কে।’ বললুম, ‘নাম দিয়ে দিলে বুঝি?’ সে বললে, ‘হ্যাঁ।’ বললুম, ‘বেশ করেছ, এত লোক থাকতে তুমি আমারই নাম দিতে গেলে কেন? এবার আমার নামে কেস করলেই মারা পড়েছি।’ চিরকালের ভীতু আমি, ভয় পেয়েছিলুম বই কি একটু।
‘পথে বিপথে’র জাহাজী গল্পগুলি আমি তখনই লিখি। স্টীমারের সেই সব ক্যারেকটারই গেঁথে গেঁথে দিয়েছি তাতে। অনেক দিন বাদে ভাদরের ভরা গঙ্গার ছবি এঁকেছিলুম দু-চারখানি। একজিবিশনে দিয়েছিলুম, কোথায় গেল তা কে জানে। একখানি মনে আছে, রুমানিয়ার রাজা নিলেন, গঙ্গার ছবি রুমানিয়ার রাজা নিয়ে চলে গেলেন, দেশি লোকের নজরই পড়ল না তাতে, অথচ মা গঙ্গা মা গঙ্গা বলে আমরা চেঁচিয়ে আওড়াই খুব—বন্দ মাতা সুরধুনী, পুরাণে মহিমা শুনি, পতিতপাবনী পুরাতনী। আর ডুব দিয়ে দিয়ে উঠি আমাদের সেই ডারবির ঘোড়া ওঠার মতন।
১৭. ছবি আঁকা শিখতে কদিন লাগে
ছবি আঁকা শিখতে কদিন লাগে? বেশি দিন না, ছ-মাস, আমি শিখিয়েছিও তাই। ছ-মাসে আমি আর্টিস্ট তৈরি করে দিয়েছি। এর বেশি সময় লাগা উচিত নয়। এরই মধ্যে যাদের হবার হয়ে যায়—আর যাদের হবে না তাদের বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত; হ্যাঁ, মানি যে ডিম ফুটে বাচ্চা বের হতে একটা নির্ধারিত সময় লাগে—তার পরে, ব্যস, উড়ে যাও, হাঁসের বাচ্চা হও তো, জলে ভাস। ছবি আঁকবে তুমি নিজে, মাস্টারমশায় তার ভুল ঠিক করে দেবেন কি? তুমি যে রকম গাছের ডাল দেখেছ তাই এঁকেছ। মাস্টার মশায়ের মতন ডাল আঁকতে যাবে কেন? তরকারিতে নুন বেশি হয়, ফেলে দিয়ে আবার রান্না কর; পায়েসে মিষ্টি কম হয়, মিষ্টি আরো দাও। ছবিতেও ভুল হয়,—ফেলে দিয়ে আবার নতুন ছবি আঁক। বারে বারে একই বিষয় নিয়ে আঁক। আমি হলে তো তাই করতুম। ছবিতে আবার ভুল শুধরে দিয়ে জোড়াতাড়া দেওয়া, ও কিরকম শেখানো? দরকার হয়, আর একটু নুন দিতে পার। দরকার হয় একটু চিনি, তাও দিতে পার। কিন্তু গাছের ডালটা এমনি হবে, পা-টা এমনি করে আঁকতে হবে, এ রকম করে শেখাবার আমি মোটেই পক্ষপাতী নই। আমি নন্দলালদের অমনি করেই শিখিয়েছি। তবে ছাত্রকে সাহস দিতে হয়। তাদের বলতে হয়, এঁকে যাও, কিছু এদিক ওদিক হয় তো আমি আছি।
এই কথাই বলেছিলেন রবিকাকা আমার লেখার বেলায়। একদিন আমায় উনি বললেন, ‘তুমি লেখো না, যেমন করে তুমি মুখে গল্প কর তেমনি করেই লেখো।’ আমি ভাবলুম, বাপ রে লেখা—সে আমার দ্বারা কস্মিন্ কালেও হবে না। উনি বললেন, ‘তুমি লেখোই না; ভাষায় কিছু দোষ হয় আমিই তো আছি।’ সেই কথাতেই মনে জোর পেলুম। একদিন সাহস করে বসে গেলুম লিখতে। লিখলাম এক ঝোঁকে একদম শকুন্তলা বইখানা। লিখে নিয়ে গেলুম রবিকাকার কাছে, পড়লেন আগাগোড়া বইখানা, ভালো করেই পড়লেন। শুধু একটি কথা ‘পল্বলের জল’, ওই একটিমাত্র কথা লিখেছিলেম সংস্কৃতে। কথাটা কাটতে গিয়ে ‘না থাক্’ বলে রেখে দিলেন। আমি ভাবলুম, যা। সেই প্রথম জানলুম, আমার বাংলা বই লেখবার ক্ষমতা আছে। এত যে অজ্ঞতার ভিতরে ছিলুম, তা থেকে বাইরে বেরিয়ে এলুম। মনে বড় ফূর্তি হল, নিজের উপর মস্ত বিশ্বাস এল। তার পর পটাপট করে লিখে যেতে লাগলুম—ক্ষীরের পুতুল, রাজকাহিনী ইত্যাদি। সেই যে উনি সেদিন বলেছিলেন ‘ভয় কি আমিই তো আছি সেই জোরেই আমার গল্প লেখার দিকটা খুলে গেল।
কিন্তু আমার ছবির বেলায় তা হয়নি—বিফলতার পর বিফলতা। তাই তো এদের বলি, শেখা জিনিসটা কি? কিছুই না, কেবলই মনে হবে, কিছুই হল না; আমার সেই দুঃখের কথাটাই বলি। শেখা, ওকি সহজ জিনিস? কি কষ্ট করে যে আমি ছবি আঁকা শিখেছি। তোমাদের মতন নয়, দিব্যি আরামের ঘর, কয়েক ঘণ্টা গিয়ে বসলুম, কিছু করলুম, মাস্টারমশায় এসে ভুলটুল শুধরে দিয়ে গেলেন। আর্টস্ট চিরদিনই শিখছে, আমার এখনো বছরের পর বছর শেখাই চলছে। যদিও ছেলেবেলা থেকেই আমার শিল্পীজীবনের শুরু, কিন্তু কি করে কি ভাবে তা এল আমি নিজেই জানিনে। দাদা সেন্ট জেভিয়ারে রীতিমত ছবি আঁকা শিখতেন, ছবি এঁকে পুরস্কারও পেয়েছিলেন। সত্যদাদা হরিনারায়ণবাবুর কাছে বাড়িতে তেলরঙের ছবি আঁকতেন, দাদাকেও হরিবাবু শেখাতেন। মেজদা, নিরুদা, আমার পিসতুত ভাই, তাঁরও শখ ছিল ঘড়ি মেরামতের আর হাতির দাঁতের উপর কাজ করবার। একতলার ঘরে এসে তিনি হাতির দাঁতে ছবি আঁকতেন; এক দিল্লিওয়ালা আসত তাঁকে শেখাতে। মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে উকিঝুঁকি দিতুম, ভারি ভালো লাগত। হিন্দু মেলায় যে দিল্লির মিনিয়েচার দেখেছিলুম এই লোকটিই দেখিয়েছিল তা। সেও চোখ ভুলিয়েছিল তখন। সেই সময়ে আঁকতে জানতুম না তো সেরকম কিছু, তবে রং নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতুম; ইচ্ছে করত, আমিও রং তুলি দিয়ে এটা ওটা আঁকি। আঁকার ইচ্ছে ছোটবেলা থেকেই জেগেছিল। এর বহুকাল পরে বড় হয়েছি, বিয়ে হয়েছে, বড় মেয়ে জন্মেছে, সেই সময় একদিন খেয়াল হল ‘স্বপ্নপ্রয়াণ’টা চিত্রিত করা যাক। এর আগে ইস্কুলে পড়তেও কিছু কিছু আঁকা অভ্যেস ছিল। সংস্কৃত কলেজে অনুকূল আমায় লক্ষ্মী সরস্বতী আঁকা শিখিয়েছিল। বলতে গেলে সেই-ই আমার প্রথম শিল্পশিক্ষার মাস্টার, সূত্রপাত করিয়ে দিয়েছিল ছবি আঁকার।
তা স্বপ্নপ্রয়াণের ছবি আঁকবার যখন খেয়াল হল, তখন আমি ছবি আঁকায় একটু একটু পেকেছি। কি করে যে পাকলুম মনে নেই, তবে নিজের ক্ষমতা জাহির করার চেষ্টা আরম্ভ হল স্বপ্নপ্রয়াণ থেকে। ‘স্বপন-রমণী আইল অমনি, নিঃশব্দে যেমন সন্ধ্যা করে পদার্পণ’ এমনি সব ছবি, তখন সত্যি যেন ‘খুলে দিল মনোমন্দিরের চাবি’। ছবিখানি ‘সাধনা’ কাগজে বেরিয়েছিল। যাই হোক, স্বপ্নপ্রয়াণটা তো অনেকখানি এঁকে ফেললুম। মেজমা আমাদের উৎসাহ দিতেন। ‘বালক’ কাগজের জন্য লিথোগ্রাফ প্রেস করে দিলেন তাঁর বাড়িতে। যার যা কিছু আঁকার শখ লেখার শখ ছিল, মায় রবিকাসুদ্ধ, সবাই তাঁর কাছে যেতুম। মেজমা আমার স্বপ্নপ্রয়াণের ছবিগুলো দেখে ধরে বসলেন, ‘অবন, তোমাকে রীতিমত ছবি আঁকা শিখতে হবে।’ উনিই ধরে বেঁধে শিল্পকাজে লাগিয়ে দিলেন।
আমারও ইচ্ছে হল ছবি আঁকা শিখতে হবে। তখন ইউরোপীয়ান আর্ট ছাড়া গতি ছিল না। ভারতীয় শিল্পের নামও জানত না কেউ। গিলার্ডি আর্ট স্কুলের ভাইসপ্রিন্সিপাল, ইটালিয়ান আর্টিস্ট—মেজমা কুমুদ চৌধুরীকে বললেন, ‘তুমি অবনকে নিয়ে তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও, আর শেখার বন্দোবস্তও কর।’ মাকে জিজ্ঞেস করলুম। মা বললেন, ‘কোনো কাজ তে করছিসনে, স্কুল ছেড়ে দিয়েছিস, তা শেখ্ না। একটা কিছু নিয়ে থাকবি ভালোই তো।’ ব্যবস্থা হল, এক-একটা lessonএর জন্যে কুড়ি টাকা দিতে হবে, মাসে তিন-চারটে পাঠ দিতেন তাঁর বাড়িতেই। খুব যত্ন করেই শেখাতেন আমায়। তাঁর কাছে গাছ ডালপাতা এই সব আঁকতে শিখলুম। প্যাস্টেলের কাজও তিনি যত্ন করে শেখালেন। তেলরঙের কাজ, প্রতিকৃতি আঁকা, এই পর্যন্ত উঠলুম সেখানে। ছবি শেখার হাতে খড়ি হল সেই ইটালিয়ান মাস্টারের কাছে। কিছুদিন যায়, দেখি, তাঁর কাছে হাতে খড়ির পর বিদ্যে আর এগোয় না। তেলরঙের কাজ যখন আরম্ভ করলুম, দেখি, ইটালিয়ান ধরনে আর চলে না। বাঁধা গতের মত তুলি দিয়ে ধীরে ধীরে আঁকা, সে আর পোষাল না। আগে গাছপালা আঁকার মধ্যে তবু কিছু আনন্দ পেতুম। কিন্তু ধরে ধরে আর্ট স্কুলের রীতিতে তুলি টানা আর রং মেলানো, তা আর কিছুতেই পেরে উঠলুম না। ছ-মাসের মধ্যেই স্টুডিয়োর সমস্ত শিক্ষা শেষ করে সরে পড়লুম।
বিয়ে হয়েছে, রীতিমত ঘরসংসার আরম্ভ করেছি, কিন্তু ছবি আঁকার ঝোঁকটা কিছুতেই গেল না। তখন এই পর্যন্ত আমার বিদ্যে ছিল যে নর্থ লাইট মডেল না হলে ছবি আঁকা যায় না। আর স্টুডিয়ো না হলে আর্টিস্ট ছবি আঁকবে কোথায় বসে? উত্তর দিকের ঘর বেছে বাড়িতেই স্টুডিয়ো সাজালুম। নর্থ লাইট, সাউথ লাইট ঠিক করে নিয়ে পর্দা টানালুম জানালায় দরজায় স্কাই লাইটে। বসলুম পাকাপাকি স্টুডিয়ো ফেঁদে। রবিকা খুব উৎসাহ দিলেন। সেই স্টুডিয়োতেই সেই সময় রবিকা চিত্রাঙ্গদার ছবি আঁকতে আমায় নির্দেশ দিচ্ছেন ফটোতে দেখেছ তো? চিত্রাঙ্গদা তখন সবে লেখা হয়েছে। রবিকা বললেন, ছবি দিতে হবে। আমার তখন একটু সাহসও হয়েছে, বললুম, রাজি আছি। সেই সময় চিত্রাঙ্গদার সমস্ত ছবি নিজ হাতে এঁকেছি, ট্রেস করেছি। চিত্রাঙ্গদা প্রকাশিত হল। এখন অবশ্য সে সব ছবি দেখলে আমার হাসি পায়। কিন্তু এই হল রবিকার সঙ্গে আমার প্রথম আর্ট নিয়ে যোগ। তার পর থেকে এতকাল রবিকার সঙ্গে বহুবার আর্টের ক্ষেত্রে যোগাযোগ হয়েছে, প্রেরণা পেয়েছি তাঁর কাছ থেকে। আজ মনে হচ্ছে আমি যা কিছু করতে পেরেছি তার মূলে ছিল তার প্রেরণা। সেই সময়ে রবিকার চেহারা আমি অনেক এঁকেছি, ভালো করে শিখেছিলুম প্যাস্টেল ড্রইং। নিজের স্টুডিয়োতে যাকে পেতুম ধরে ধরে প্যাস্টেলে অাঁকতুম। অক্ষয়বাবু, মতিবাবু, সবার ছবি করেছি, মহৰ্ষির পর্যন্ত। এই করে করে পোর্টেটে হাত পাকালুম। রবিকাকেও প্যাস্টেলে আঁকলুম, জগদীশবাবু সেটি নিয়ে নিলেন।
সেই সময়ে রবিবৰ্মা আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। তখন আমি নতুন আর্টিস্ট—তিনি আমার স্টুডিয়োতে আমার কাজ দেখে খুব খুশি হয়েছিলেন। বলেছিলেন, ছবির দিকে এর ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল। আমি কোথায় বেরিয়ে গিয়েছিলুম, বাড়িতে ছিলুম না, ফিরে এসে শুনলুম বাড়ির লোকের মুখে।
প্যাস্টেলে হাত পাকল, মনও বেগড়াতে আরম্ভ করল, শুধু প্যাস্টেল আর ভালো লাগে না। ভাবলুম, অয়েলপেন্টিং শিখতে হবে। ধরলুম এক ইংরেজ আর্টিস্টকে। নাম সি. এল. পামার। তাঁর কাছে যাই, পয়সা খরচ করে খাস বিলেতি গোরা মডেল আনি, মানুষ আঁকতে শিখি। একদিন এক গোরাকে নিয়ে এল আমার চাপরাসি স্টুডিয়োতে মডেল হবার জন্য। সে এসেই তড়বড় করে তার গায়ের জামা সব কটা খুলে এবারে প্যান্টও খুলতে যায়। চেঁচিয়ে উঠলুম, ‘হাঁ হাঁ, কর কি। প্যান্ট তোমার আর খুলতে হবে না।’ প্যান্ট খুলবেই সে, বলে, ‘তা নইলে তোমরা আমাকে কম টাকা দেবে।’ পামারকে বললুম, ‘সাহেব, তুমি বুঝিয়ে বল, টাকা ঠিকই দেব। প্যাণ্ট যেন না খুলে ফেলে, ওর খালি গা’ই যথেষ্ট।’ সাহেব শেষে তাকে বুঝিয়ে শান্ত করে। আর একবার এক অ্যাংলোইণ্ডিয়ান মেম এল মডেল হতে, তার পোর্টেট আঁকলুম, মেম তা দেখে টাকার বদলে সেই ছবিখানাই চেয়ে বসলে; বললে, ‘আমি টাকা চাইনে, এই ছবিখানা আমাকে দিতেই হবে, নইলে নড়ব না এখান থেকে।’ আমি তো ভাবনায় পড়লুম, কি করি। সাহেব বললে, ‘তা বই কি, ছবি দিতে পারবে না ওকে।’ বলে দিলেন দুই ধমক লাগিয়ে; মেম তখন সুড় সুড় করে নেমে গেল নিচে। এই রকম আর কিছুদিনের মধ্যেই ওঁদের আর্টের তৈলচিত্রের করণ-কৌশলটা তো শিখলাম। তখন একদিন সাহেব মাস্টার একটা মডেলের কোমর পর্যন্ত আঁকতে দিলেন। বললেন, ‘এক সিটিঙে দু-ঘণ্টার মধ্যে ছবিখানা শেষ করতে হবে।’ দিলুম শেষ করে। সাহেব বললেন, ‘চমৎকার উতরে গেছে—passed with credit।’ আমি বললুম, ‘তা তো হল, এখন আমি করব কি?’ সাহেব বললেন, ‘আমার যা শেখাবার তা আমি তোমায় শিখিয়ে দিয়েছি। এবারে তোমার অ্যানাটমি স্টাডি করা দরকার।’ এই বলে একটি মড়ার মাথা আঁকতে দিলেন। সেটা দেখেই আমার মনে হল যেন কি একটা রোগের বীজ আমার দিকে হাওয়ায় ভেসে আসছে। সাহেবকে বললুম, ‘আমার যেন কি রকম মনে হচ্ছে।’ সাহেব বললেন, ‘No, you must do it—তোমাকে এটা করতেই হবে।’ সারাক্ষণ গা ঘিন ঘিন করতে লাগল। কোনোরকমে শেষ করে দিয়ে যখন ফিরলুম তখন ১০৬° ডিগ্রি জ্বর।
সন্ধ্যেবেলা জ্ঞান হতে দেখি ঘরের বাতিগুলো নিবন্ত প্রদীপের মত মিটমিট করছে। মা জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছিল। মাকে মড়ার মাথার ঘটনা বললুম। মা তখনকার মত ছবি আঁকা আমার বন্ধ করে দিলেন, বললেন, কাজ নেই আর ছবি আঁকায়। তখন আমার কিছুকালের জন্য ছবি আঁকা বন্ধ ছিল। তার পরে একজন ফ্রেঞ্চ পড়াবার মাস্টার এলেন আমাদের জন্য, নাম তার হ্যামারগ্রেন। রামমোহন রায়ের নাম শুনে তাঁর দেশ নরওয়ে থেকে হেঁটে এদেশে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর কাছে একটু একটু ফ্রেঞ্চ পড়তুম, তিনি খুব ভাল পড়াতেন। কিন্তু পড়ার সময়ে খাতার মার্জিনে তার নাক মুখের ছবিই আঁকতুম বসে বসে। তাই আর আমার ফ্রেঞ্চ পড়া এগল না। এদেশেই তিনি মারা যান। মারা যাবার পরে আমার খাতার সেই নোটগুলো দেখে পরে তাঁর ছবি আঁকি। বহুদিন পরে সেদিন রবিকাকা বললেন যে নরওয়েতে তাঁর মিউজিয়াম হচ্ছে, যদি তোমার কাছে তাঁর ছবি থাকে তবে তারা চাচ্ছে। তাঁর চেহার কারো কাছে ছিল না। আমি পুরাতন বাক্স খুঁজে সেই ছবি বের করে পাঠাই, তার আত্মীয়-স্বজন খুব খুশি হয়ে আমাকে চিঠি দিয়েছিলেন। ভাগ্যিস তাঁর চেহারা নোট করে রেখেছিলুম।
যাক ওকথা। তেলরঙ তো হল। এবার জলরঙের কাজ শেখবার ইচ্ছে। মাকে বলে আবার তাঁর কাছেই ভরতি হলুম। এখন ল্যাণ্ডস্কেপ আর্টিস্ট হয়ে, ঘাড়ে ‘ইজেল’ বগলে রঙের বাক্স নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। কিন্তু কতকাল চলবে আর এমনি করে? তবু মুঙ্গেরের ওদিকে ঘুরে ঘুরে অনেকগুলি দৃশ্য এঁকেছিলুম।
কিছুদিন তো চলল এমনি করে, মন আর ভরে না। ছবি তো এঁকে যাচ্ছি, কিন্তু মন ভরছে কই? কি করি ভাবছি, রোজই ভাবি কি করা যায়। এদিকে স্টুডিয়ো হয়ে উঠল তামাক খাবার আর দিবানিদ্রার আড্ডা। এমন সময়ে এক ঘটনা। শুনতেম আমার ছোটদাদামশায়ের চেহারা অতি সুন্দর ছিল, কিন্তু আমাদের কাছে তার একখানাও ছবি ছিল না। আমি তাঁর ছবির জন্য খোঁজখবর করছিলুম নানা জায়গায়। তখন বিলেত থেকে এক মেম মিসেস মার্টিনডেল খবর পেয়ে লিখলেন, ‘তুমি তাঁরই নাতি? বড় খুশি হলুম। তাঁর সঙ্গে আমার বড় ভাব ছিল। তোমার বিয়েথাওয়া হয়েছে! তোমার মেয়ের জন্য আমি একটা পুতুল পাঠাচ্ছি।’ বলে প্রকাণ্ড একটা বিলিতি ডল নেলিকে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি তখন খুবই বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু কি রকম আশ্চর্য তাঁর মন ছিল; কোন্কালে আমার ছোটদাদামশায়ের সঙ্গে তাঁর ভাব ছিল, সেই সূত্রে আমাকে না দেখেও তিনি নগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতি বলেই স্নেহ করতে চাইতেন। তিনি বিলেত থেকে লিখলেন, ‘তোমার আর্টের দিকে ঝোঁক আছে,—আমিও একটু আধটু অাঁকতে পারি। বলো তোমার জন্য আমি কিছু করতে পারি কিনা।’ তিনি আরো লিখলেন, ‘তুমি যদি কিছু দাও তো তার চারদিকে ইলুমিনেট করিয়ে দিতে পারি।’ বইয়ের লেখার চারদিকে নকশা অাঁকা থাকে, খুব পুরোনো আর্ট ওঁদের, তাই একটা এঁকে পাঠাবেন। ভাবলুম, তা মন্দ নয় তো। তিনি বলেছিলেন, ‘আমি গরিব, এজন্য কিছু দিতে হবে।’ পাঠিয়েছিলুম কিছু দশ কি বারো পাউণ্ড মনে নেই ঠিক। আইরিশ মেলডিজের কবিতা ছোটদাদামশায়ের বড় প্রিয় জিনিস ছিল। ভাবলুম, সেটাই যত্ন করে রাখবার বস্তু হয়ে আসুক। কিছুকাল বাদে তিনি পাঠিয়ে দিলেন দশ-বারোখানা বেশ বড় বড় ছবি—সে কি সুন্দর, কি বলব তোমায়। থ হয়ে গেলুম ছবি দেখে।
আবার হবি তো হ সেই সময়ে আমার ভগ্নীপতি শেষেন্দ্র, প্রতিমার বাবা, একখানা পার্শিয়ান ছবির বই দিল্লির, আমাকে বকশিশ দিলেন। রবিকাকাও আবার সে সময়ে রবিবর্মার ছবির কতকগুলি ফোটো আমাকে দিলেন। তখন রবিবর্মার ছবিই ছিল কিনা ভারতীয় চিত্রের আদর্শ। যাই হোক তখন সেই আইরিশ মেলডির ছবি ও দিল্লির ইন্দ্রসভার নকশা যেন আমার চোখ খুলে দিলে। একদিকে আমার পুরাতন ইউরোপীয়ান আর্টের নিদর্শন ও আর একদিকে এদেশের পুরাতন চিত্রের নিদর্শন। দুই দিকের দুই পুরাতন চিত্রকলার গোড়াকার কথা একই। সে যে আমার কি আনন্দ, সেই সময়ে সাধনাতে আমার ওই ইন্দ্রসভার বইখানির বর্ণনা দিয়ে ‘দিল্লির চিত্রশালিকা’ ব’লে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবন্ধ লিখেছিলেন; চারদিকে তখন একটা সাড়া পড়ে গিয়েছিল।
যাক, ভারতশিল্পের তো একটা উদ্দিশ পেলুম। এখন শুরু করা যাবে কি করে কাজ? তখন একতলার বড় ঘরটাতে একধারে চলেছে বিলিয়ার্ড খেলার হো হো, একধারে আমি বসেছি রং তুলি নিয়ে আঁকতে। দেশের শিল্পের রাস্তা তো পেয়ে গেছি, এখন আঁকব কি? রবিকাকা আমায় বললেন, বৈষ্ণব পদাবলী পড়ে ছবি আঁকতে। রবিকাকা আমাকে এই পর্যন্ত বাতলে দিলেন যে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির কবিতাকে রূপ দিতে হবে। লেগে গেলুম পদাবলী পড়তে। প্রথম ছবি করি ভারতীয় পদ্ধতিতে চণ্ডীদাসের দু-লাইন কবিতা—
পৌখলী রজনী পবন বহে মন্দ
চৌদিকে হিমকর, হিম করে ফন্দ।
এ ছবিটা এখনো আমার কাছেই বাক্সবন্ধ। সেই আমার প্রথম দেশী ধরনের ছবি ‘শুক্লাভিসার’। কিন্তু দেশী রাধিকা হল না, সে হল যেন মেমসাহেবকে শাড়ি পরিয়ে শীতের রাত্তিরে ছেড়ে দিয়েছি। বড় মুষড়ে গেলুম—নাঃ, ও হবে না, দেশী টেকনিক শিখতে হবে। তখন তারই দিকে ঝোঁক দিলুম। ছবিতে সোনাও লাগাতে হবে। তখনকার দিনে রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়িতে এক মিস্ত্রি ফ্রেমের কাজ করে। লোকটির নাম পবন, আমার নাম অবন। তাকে ডেকে বললুম, ‘ওহে সাঙাত, পবনে অবনে মিলে গেছে, শিখিয়ে দাও এবারে সোনা লাগায় কি করে।’ সে বললে, ‘সে কি বাবু, আপনি ও কাজ শিখে কি করবেন? আমাকে বলবেন আমি করে দেব।’ ‘না হে, আমার ছবিতে সোনা লাগাব; আমাকে শিখিয়ে দাও।’ শিখলাম তার কাছে কি করে সোনা লাগাতে হয়। সবরকম টেকনিক তো শেখ হল, তার পর আমাকে পায় কে? বৈষ্ণব পদাবলীর এক সেট ছবি সোনার রূপোর তবক ধরিয়ে এঁকে ফেললুম। তারপর ‘বেতালপঞ্চবিংশতি’ অাঁকতে শুরু করলুম। সেই পদ্মাবতী পদ্মফুল নিয়ে বসে আছে, রাজপুত্তুর গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে; আর অন্যগুলিও। যাক রাস্তা পেলুম, চলতেও শিখলুম, এখন হু হু করে এগোতে হবে। তখন এক-একখানি করে বই ধরছি আর কুড়ি-পঁচিশখানা করে ছবি এঁকে যাচ্ছি। তাই যখন হল কিছুকাল গেল এমনি।
তখন কি আর ছবির জন্য ভাবি, চোখ বুজলেই ছবি আমি দেখতে পাই—তার রূপ, তার রেখা, মায় প্রত্যেক রঙের শেড পর্যন্ত। তখন যে আমার কি অবস্থা বোঝাব কি তোমায়। ছবিতে আমার তখন মনপ্রাণ ভরপুর, হাত লাগাতেই এক-একখানা ছবি হয়ে যাচ্ছে।
হু হু করে ছবি হতে লাগল। কৃষ্ণচরিত্র, বুদ্ধচরিত্র, বেতালপঞ্চবিংশতি ইত্যাদি। নিচের তলার দালানটাতে বসে মশগুল হয়ে ছবি আঁকতুম। আমি যখন কৃষ্ণের ছবি আঁকছি তখন শিশির ঘোষ মশায় ছিলেন পরম বৈষ্ণব। একদিন তিনি এলেন কৃষ্ণের ছবি দেখতে। আমি নিচের তলার ঘরটিতে বসে নিবিষ্টমনে ছবি আঁকছি, মুখ তুলে দেখি দরজার পাশে একটি অচেনা মুখ উঁকিঝুঁকি মারছে। আমি বললাম, ‘কে হে।’ তিনি বললেন, ‘আমি শিশির ঘোষ। তুমি কৃষ্ণের ছবি আঁকছ তাই শুনে দেখতে এলুম।’ আমি তাড়াতাড়ি উঠে ‘আসুন আসুন’ বলে তাঁকে ঘরে এনে ভাল করে বসিয়ে ছবিগুলি সব এক এক করে দেখাতে লাগলুম। তিনি সবগুলি দেখলেন, শেষে হেসে বললেন, “হুঁ, কি এঁকেছ তুমি? এ কি রাধাকৃষ্ণের ছবি? লম্বা লম্বা সরু সরু হাত পা যেন কাটখোট্টাই—এই কি গড়ন? রাধার হাত হবে নিটোল, নধর তাঁর শরীর। জান না তার রূপবর্ণনা?’ এই বলে তিনি চলে গেলেন। আমি খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে রইলুম কিন্তু তার কথায় মনে কোনো দাগ কাটল না। ছবি করে যেতে লাগলুম। তখন আমি বিলিতি ছবির কাগজ পড়িও না, দেখিও না, ভয় পাছে বিলিতি আর্টের ছোঁয়াচ লাগে। গানবাজনা আর ছবি নিয়ে মেতে ছিলুম। দিনরাত কেবল এসরাজ বাজাই, ছবি আঁকি।
সেই সময়ে কলকাতায় লাগল প্লেগ। চারদিকে মহামারী চলছে, ঘরে ঘরে লোক মরে শেষ হয়ে যাচ্ছে। রবিকাকা এবং আমরা এবাড়ির সবাই মিলে চাঁদা তুলে প্লেগ হাসপাতাল খুলেছি, চুন বিলি করছি। রবিকাকা ও সিস্টার নিবেদিতা পাড়ায় পাড়ায় ইন্পেক্শনে যেতেন। নার্স ডাক্তার সব রাখা হয়েছিল। সেই প্লেগ লাগল আমারও মনে। ছবি আঁকার দিকে না ঘেঁষে আরো গানবাজনায় মন দিলুম। চারদিকে প্লেগ আর আমি বসে বাজনা বাজাই। হবি তো হ, সেই প্লেগ এসে ঢুকল আমারই ঘরে। আমার ছোট্ট মেয়েটাকে নিয়ে গেল। ফুলের মতন মেয়েটি ছিল, বড় আদরের। আমার মা বলতেন, ‘এই মেয়েটিই অবনের সবচেয়ে সুন্দর।’ ন-দশ বছরের মেয়েটি আমার টুক করে চলে গেল; বুকটা ভেঙে গেল। কিছুতে আর মন যায় না। এ বাড়ি ছেড়ে—চৌরঙ্গিতে একটা বাড়িতে আমরা পালিয়ে গেলুম। সেখানে থাকি, একটা টিয়েপাখি কিনলুম, তাকে ছোলা ছাতু খাওয়াই, মেয়ের মাও খাওয়ায়। পাখিটাকে বুলি শেখাই। দুঃখ ভোলাবার সাথি হল পাখির ছানাটা; নাম দিলেম তার চঞ্চু, মায়ের কোলছাড়া টিয়াপাখির ছানা।
সে সময়ে ঘুড়ি ওড়াবারও একটা নেশা চেপেছিল। পাশের বাড়ির মিসেস্ হায়ার বলে এক বুড়ি ইহুদী মেমসাহেবের সঙ্গে আলাপ হল। আমাকে খুব যত্ন করতেন, কতরকম রান্না করে খাওয়াতেন। তাঁর সুন্দর একটি বাগান ছিল; ছাগলের জন্য দিব্য বেড়া দিয়ে ঘেরা পাহাড়। খুব বড় ঘরের সেকেলে ইহুদী পরিবার। মায়ের সঙ্গে বুড়ি ইহুদী মেমের কথা হত; মাঝে মাঝে আমার জন্যে ভালো সুগন্ধি তামাকও পাঠাত। সেখানে তো এমনি করে আমার দিন যাচ্ছে। সে সময়ে মেজমার কাছে যাওয়া-আসাতে হ্যাভেল সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়। একদিন মেজমা আমাকে ধরে বসলেন, ‘তোমাকে আর্ট স্কুলে যেতে হবে। হ্যাভেল তোমাকে ভাইসপ্রিন্সিপ্যাল করতে চান।’ আমার তখন কি কাজকর্ম করবার মত অবস্থা? আমি সাহেবকে বললুম সে কথা। তিনি আমার জ্যেষ্ঠের মতন ছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, ‘তুমি করছ কি? You do your work—your work is your only medicine, তুমি তোমার কাজ কর, কাজই তোমার ওষুধ।’ তাঁকে চিরকাল গুরু বলে শ্রদ্ধা করেছি, জ্যেষ্ঠের মত ভক্তি করেছি কি সাধে? তিনিও আমাকে collaborator সহকর্মী বলে ডাকতেন আদর করে; কখনো চেলাও বলেছেন। ছোট ভাইয়ের মত ভালোবাসতেন। আমি নন্দলালকে যতখানি ভালোবাসি তার বেশি তিনি আমাকে ভালোবাসতেন।
সে তো গেল, কিন্তু আমি চাকরি করব কি? ঠিকসময়ে হাজিরা দিতে হবে; এদিকে দিনে সাতবার করে তামাক খাওয়া আমার অভ্যাস, তার উপরে শরীর তখন খারাপ। মাকে বললুম, ‘সে আমি পারব না মা, তুমি যা হয় বল সাহেবকে।’ সাহেব ইংরেজের বাচ্চা, নাছোড়বান্দা। বলে পাঠালেন মাকে, ‘তোমার ছেলের সব ভার আমার। তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কোনো অভাব হবে না। দুপুরে আমি তার খাওয়ার ভার নিলাম, তামাক সে যতবার ইচ্ছে খাবে। আমি বলছি আমি তার শরীর ভালো করে দেব।’ কিছুতেই ছাড়ে না, আমাকে রাজি হতেই হল। কিন্তু ভয় হল আমি শেখাব কি? নিজেই বা কি জানি। সাহেব তাতেও বললেন, ‘সে আমি দেখব’খন। তোমার কিছু ভাবতে হবে না। তুমি শুধু নিজের কাজ করে যাবে। তুমি কত টাকা মাসে চাও বল।’ আমি বললুম, ‘সে আর আমি কি বলব সাহেব, সবই তো তুমি জানো, এও তুমিই জানবে। কি দেবে না-দেবে সেও তোমার ইচ্ছা, আমি চাইনে কিছুই।’ সাহেব বললেন, ‘আচ্ছা, তোমাকে আমি ভাইসপ্রিন্সিপাল করে দিলাম। তুমি এখন মাসে তিনশো টাকা করে পাবে।’
যেতে শুরু করে দিলাম সকাল সকাল চারটি ভাত খেয়ে। প্রথম দিন গিয়ে তো আপিসঘরে ঢুকে মুষড়ে গেলুম—আমি তো আপিসের কাজ বলতে কিছুই জানি না। সাহেব বললেন, ‘কে বলে তোমার ওসব কাজ করতে হবে? তার জন্যে হেডমাস্টার, হেডক্লার্ক আছে। তারা সব দেখবে আপিসের কাজ। তুমি তোমার কাজ করে যাও। চল, তোমাকে আর্ট গ্যালারি দেখিয়ে নিয়ে আসি।’ আমাকে নিয়ে গেলেন আর্ট গ্যালারি দেখাতে, আমি আর সাহেব চলেছি, আগে-পিছে চাপরাসি মস্ত হাতপাখা নিয়ে হাওয়া করতে করতে যাচ্ছে, বাদশাহী চালে চলেছি বড়সাহেবের আর্ট গ্যালারি দেখতে। সাহেব চাপরাসিকে বললেন পর্দা সরাতে। ভারি তো আর্ট গ্যালারি, তার আবার পর্দা সরাও—এখন ভাবলে হাসি পায়। দু-তিনখানা মোগল ছবি আর দু-একখানা পার্শিয়ান ছবি, এই খান চার-পাঁচ ছবি নিয়ে তখন আর্ট গ্যালারি। পর্দা তো সরানো হল। একটি বকপাখির ছবি, ছোটই ছবিখান, মন দিয়ে দেখছি, সাহেব পিছনে দাঁড়িয়ে বুকে হাত দিয়ে। আমাকে বললেন, ‘এই নাও এটি দিয়ে দেখ।’ বলে বুকপকেট থেকে একটি আতসী কাঁচ বের করে দিলেন।
সেই কাঁচটি পরে আর আমি হাতছাড়া করিনি। বহুকাল সেটি আমার জামার বুকপকেটে ঘুরেছে। আমি নন্দলালদের বলতুম, এটি আমার দিব্যচক্ষু। সেই কাঁচ চোখের কাছে ধরে বকের ছবিটি দেখতে লাগলুম। ওমা কি দেখি, এ তে সামান্য একটুখানি বকের ছবি নয়, এ যে আস্ত একটি জ্যান্ত বক এনে বসিয়ে দিয়েছে। কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখি, তার প্রতিটি পালকে কি কাজ। পায়ের কাছে কেমন খসখসে চামড়া, ধারালো নখ, তার গায়ের ছোট্ট ছোট্ট পালক—কি দেখি—আমি অবাক হয়ে গেলুম, মুখে কথাটি নেই। পিছনে সাহেব তেমনি ভাবে বুকে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে, আমার অবস্থা দেখে মুচকি মুচকি হাসছেন, যেন উনি জানতেন যে আমি এমনি হয়ে যাব এ ছবি দেখে। তার পর আর দু-চারখানা ছবি যা ছিল দেখলুম। সবই ওই একই ব্যাপার। মাথা ঘুরে গেল। তবে তো আমাদের আর্টে এমন জিনিসও আছে, মিছে ভেবে মরছিলুম এতকাল। পুরাতন ছবিতে দেখলুম ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি, ঢেলে দিয়েছে সোনা রুপো সব। কিন্তু একটি জায়গায় ফাঁকা, তা হচ্ছে ভাব। সবই দিয়েছে ঐশ্বর্যে ভরে, কোথাও কোনো কার্পণ্য নেই কিন্তু ভাব দিতে পারেনি। মানুষ আঁকতে সবই যেন সাজিয়ে গুজিয়ে পুতুল বসিয়ে রেখেছে। আমি দেখলুম এইবারে আমার পালা। ঐশ্বর্য পেলুম, কি করে তার ব্যবহার তা জানলুম, এবারে ছবিতে ভাব দিতে হবে।
বাড়ি এসে বসে গেলুম ছবি আঁকতে। আঁকলুম ‘শাজাহানের মৃত্যু’।
এই ছবিটি এত ভালো হয়েছে কি সাধে? মেয়ের মৃত্যুর যত বেদনা বুকে ছিল সব ঢেলে দিয়ে সেই ছবি আঁকলুম। ‘শাজাহানের মৃত্যুপ্রতীক্ষা’তে যত আমার বুকের ব্যথা সব উজাড় করে ঢেলে দিলুম। যখন দিল্লির দরবার হয়, বড় বড় ও পুরাতন আর্টিস্টদের ছবির প্রদর্শনী সেখানে হবে, হ্যাভেল সাহেব আমার এই ছবিখানা আর তাজ নির্মাণের ছবি দিলেন পাঠিয়ে দিল্লি দরবারে। আমাকে দিলে বেশ বড় একটা রুপোর মেডেল, ওজনে ভারি ছিল মন্দ নয়। তার পরে যোগেশ কংগ্রেস ইণ্ডাস্ট্রিয়াল একজিবিশনে সেই ছবি পাঠিয়ে দিল, সেখানে দিল একটা সোনার মেডেল। এইরকম করে তিনচারটে মেডেল পেয়েছি, পরিনি কোনোদিন।
শাজাহানের ছবির কথা থাক্—সেই পদ্মাবতীর ছবিখানার কথা বলি। হ্যাভেল সাহেব পদ্মাবতী ও বেতালপঞ্চবিংশতির আরো তিন-চারখানি ছবি স্কুলের প্রদর্শনীতে দিলেন। পদ্মাবতী ছবিখানার দাম কত দেওয়া যায়? সাহেব দিলেন আশি টাকা দাম ধরে। লর্ড কার্জন এলেন, পদ্মাবতী দেখে পছন্দ হল তাঁর, বললেন দাম কিছু কমিয়ে দিতে। ষাট টাকার মতন দিতে চাইলেন। আমি বলি, ‘সাহেব, দিয়ে দাও, টাকামাকা চাইনে কিছু। লর্ড কার্জন চেয়েছেন ছবিখানা, সেই তো খুব দাম।’ সাহেব বললেন, ‘তুমি চুপ করে থাকো, যা বলবার বোঝাবার আমি বলব বোঝাব।’ এই বলে তিনি তাকে কি সব বোঝালেন, ছবিখানার দাম কমালেন না, লর্ড কার্জনকেও দিলেন না। আমি শেষে কি করি, পদ্মাবতীর ছবিখানা ও অন্য ছবি যে দু-তিনখানা ছিল তা হ্যাভেলকে ধরে দিয়ে বললুম, ‘এই নাও সাহেব, আমার গুরুদক্ষিণা; এগুলি আমি তোমাকে দিলুম।’ সাহেব তো লুফে নিলেন। কি খুশি হলেন, বললেন, ‘আমি এ ছবি গ্যালারিতে রেখে দেব, যত্নে থাকবে চিরকাল।’
এখন আমার মাস্টারি শুরু করার কথা বলি। সাহেব তো তার স্কুলে আমাকে নিয়ে বসালেন। সুরেন গাঙ্গুলী হল আমার প্রথম ছাত্র। সুরেনকে সাহেব তাঁত শেখাবার জন্য বেনারসে পাঠিয়েছিলেন। তাকে আবার ফিরিয়ে এনে আমাকে বললেন, ‘তুমি তোমার ক্লাস শুরু কর।’ সুরেন ও আর দু-চারটি ছেলেকে নিয়ে কাজ শুরু করে দিলাম। কিছুকাল বাদে সত্যেন বটব্যাল বলে এনগ্রেভিং ক্লাসের এক ছাত্র, একটি ছেলেকে নিয়ে এসে হাজির, বললে, ‘একে আপনার নিতে হবে।’ তখন মাস্টার কিনা, গম্ভীর ভাবে মুখ তুলে তাকালুম, দেখি কালোপানা ছোট একটি ছেলে। বললুম, ‘লেখাপড়া শিখেছ কিছু।’ বললে, ‘ম্যাট্রিক, এফ-এ পর্যন্ত পড়েছি। আমি বললুম, ‘দেখি তোমার হাতের কাজ।’ একটি ছবি দেখালে—একটি মেয়ে, পাশে হরিণ, লতাপাতা গাছগাছড়া; শকুন্তলা এঁকেছিল। এই আজকালকার ছেলেদের মতন একটু জ্যেঠামি ছিল তাতে। বললুম, ‘এ হবে না, কাল একটি সিদ্ধিদাতা গণেশের ছবি এঁকে এনো।’ পরদিন নন্দলাল এল, একটি কাঠিতে ন্যাকড়া জড়ানো, সেই ন্যাকড়ার উপরে সিদ্ধিদাতা গণেশের ছবি। বেশ এঁকেছিল প্রভাতভানুর বর্ণনা দিয়ে। বললুম ‘সাবাস’। সঙ্গে ওর শ্বশুর, দিব্যি চেহারা ছিল ওর শ্বশুরের, বললেন, ‘ছেলেটিকে আপনার হাতে দিলুম।’ আমি তাঁকে বললুম, ‘লেখাপড়া শেখালে বেশি রোজগার করতে পারবে।’ নন্দলাল জবাবে বললে, ‘লেখাপড়া শিখলে তো ত্রিশ টাকার বেশি রোজগার হবে না। এতে আমি তার বেশি রোজগার করতে পারব।’ আমি বললুম, ‘তা হলে আমার আর আপত্তি নেই।’ সেই থেকে নন্দলাল আমার কাছে রয়ে গেল। তখন একদিকে সুরেন গাঙ্গুলী এক দিকে নন্দলাল, মাঝখানে আমি বসে কাজ শুরু করে দিলুম।
এখন এক পণ্ডিত এসে জুটে গেলেন—চাকরি চাই। আমি বললুম, ‘বেশ লেগে যান, রোজ আমাদের মহাভারত রামায়ণ পড়ে শোনাবেন। আমাদের বাল্যকালের পণ্ডিত মশায়, নাম রজনী পণ্ডিত। সেই পণ্ডিত রোজ এসে রামায়ণ মহাভারত শোনাতেন। আর তাই থেকে ছবি আঁকতুম।
নন্দলাল বললে, ‘কি আঁকব?’ আমি বললুম, ‘আঁকো কর্ণের সূর্যস্তব’। ও বিষয়টা আমি চেষ্টা করেছিলুম, ঠিক হয়নি। নন্দলাল এঁকে নিয়ে এল। আমি তার উপর এই দু-তিনটে ওয়াশ দিয়ে দিলুম ছেড়ে—হাতে ধরে দেখিয়ে দেখিয়ে আমি কখনও ওকে শেখাইনি। ছবি করে নিয়ে আসত, আমি শুধু কয়েকটি ওয়াশ দিয়ে মোলায়েম করে দিতুম, কিংবা একটু আধটু রঙের টাচ্ দিয়ে দিতুম, যেমন ফুলের উপর সূর্যের আলো বুলিয়ে দেওয়া—সূর্য নয় ঠিক, আমি তো আর রবি নই, নানা রঙের মাটিরই প্রলেপ দিতেম। তখন আমাদের আঁকার কাজ তেজে চলেছে। নন্দলাল সূর্যের স্তব আঁকল তো সুরেন এদিকে রামচন্দ্রের সমুদ্রশাসন আঁকল, এই তীর ধনুক বাঁকিয়ে রামচন্দ্র উঠে রুখে দাঁড়িয়েছেন। নন্দলাল এঁকে আনল একটি মেয়ের ছবি, বেশ গড়নপিটন, টান টানা চোখ ভুরু। আমি বললুম ‘এ তো হল কৈকেয়ী, পিছনে মন্থরা বুড়ি এঁকে দাও।’ হয়ে গেল কৈকেয়ী-মন্থরা। ছবির পর ছবি বের হতে লাগল। চারদিকে তখন খুব সাড়া পড়ে গেল, ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটি খুলে গেল, হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। ইণ্ডিয়ান আর্ট শব্দ অভিধান ছেড়ে সেই প্রথম লোকের মুখে ফুটল।
আমি নিজে যখন ছবি আঁকতুম কাউকে ঘরে ঢুকতে দিতুম না, আপন মনে ছবি আঁকতুম। মাঝে মাঝে হ্যাভেল সাহেব পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকতেন পিছন দিক দিয়ে দেখে যেতেন কি করছি। চৌকি ছেড়ে উঠতে গেলে ধমকে দিতেন। আমার ক্লাসেও সেই নিয়ম করেছিলুম। দরজায় লেখা ছিল, ‘তাজিম মাফ’। আমার ছবি আঁকার পদ্ধতি ছিল এমনি। বলতুম, তোমরা একে যাও, যদি লড়াইয়ে ফতে না করতে পার, তবে এই আমি আছি—ভয় কি?
কেন বলি, যে আমার আর্টের বেলায় ক্রমাগত ব্যর্থতা? কি দুঃখ যে আমি পেয়েছি আমার ছবির জীবনে। যা ভেবেছি, যা চেয়েছি দিতে, তার কতটুকু আমি আমার ছবিতে দিতে পেরেছি? যে রঙ যে রূপ-রস মনে থাকত, চোখে ভাসত, যখন দেখতুম তার সিকি ভাগও দিতে পারলুম না তখনকার মনের অবস্থা, মনের বেদনা অবর্ণনীয়। চিরটাকাল এই দুঃখের সঙ্গে যুঝে এসেছি। ছবিতে আনন্দ আর কতটুকু পেয়েছি। শুধু দুবার আমার জীবনে আনন্দময় ভাব এসেছিল, দুবার আমি নিজেকে ভুলে বিভোর হয়ে গিয়েছিলুম, ছবিতে ও আমাতে কোনো তফাত ছিল না—আত্মহারা হয়ে ছবি এঁকেছি। একবার হয়েছিল আমার কৃষ্ণচরিত্রের ছবিগুলি যখন আঁকি। সারা মন-প্রাণ আমার কৃষ্ণের ছবিতে ভরে গিয়েছিল। চোখ বুজলেই চারিদিকে ছবি দেখি আর কাগজে হাত ছোঁয়ালেই ফস ফস করে ছবি বেরয়; কিছু ভাবতে হয় না, যা করছি তাই এক-একখানা ছবি হয়ে যাচ্ছে। তখন কৃষ্ণের সব বয়সের সব লীলার ছবি দেখতে পেতুম, প্রত্যেকটির খুঁটিনাটি রঙ সমেত। সেই ভাব আমার আর এল না।
আর একবার এসেছিল কিন্তু ক্ষণিকের জন্য। সেবারে হচ্ছে আমার মার আবির্ভাব, মৃত্যুর পর। মার ছবি একটিও ছিল না। মার ছবি কি করে আঁকা যায় একদিন বসে বসে ভাবছি, এমন সময়ে যেন আমি পরিষ্কার আমার চোখের সামনে মাকে দেখতে পেলুম। মার মুখের প্রতিটি লাইন কি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল, আমি তাড়াতাড়ি কাগজ পেনসিল নিয়ে মার মুখের ড্রইং করতে বসে গেলুম। কপাল থেকে যেই নাকের ওপর ভুরুর খাঁজ টুকতে গেছি—সে কি? মা কোথায় মিলিয়ে গেলেন। হঠাৎ যেন চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। মনে হল কে যেন আলোর সুইচটা বন্ধ করে দিলে—সব অন্ধকার। আমি চমকে বললুম, ‘দাদা, এ কি হল?’ দাদা একটু দূরে বসে ছিলেন, মুখ টিপে হাসলেন, বললেন, ‘বড় তাড়া করতে গিয়েছিলে তুমি।’ মন খারাপ হয়ে গেল। চুপচাপ বসে রইলুম, আর মনে হতে লাগল, তাই তো, এ কি হল! মা এসে এমনি করে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ ওভাবে ছিলুম, এক সময়ে দেখি আবার মায়ের আবির্ভাব। এবারে আর তাড়াহুড়ো না—স্থির হয়ে বসে রইলুম। মেঘের ভিতর দিয়ে যেমন অস্তদিনের রং দেখা যায় তেমনিতরো মায়ের মুখখানি ফুটে উঠতে লাগল। দেখলুম মাকে, খুব ভালো করে মন—প্ৰাণ ভরে মাকে দেখে নিলুম। আস্তে আস্তে ছবি মিলিয়ে গেল, কাগজে রয়ে গেল মায়ের মূর্তি। এই যে মার ছবিখানা ওই অমনি করেই আঁকা। এত ভালো মুখের ছবি আমি আর আঁকিনি ৷
আমার মুখের কথায় যদি সংশয় থাকে চাক্ষুষ প্রমাণ দেখলে তো সেদিন। সন্ধ্যের অন্ধকারে রবিকার মুখের ছবি আঁকতে বসলুম, ঝাপসা ঝাপসা অস্পষ্ট লাইন পড়ল কাগজে, তোমরাও দেখতে পাচ্ছিলে না পরিষ্কার চেহারা। আমি কিন্তু দেখলুম সুস্পষ্ট চেহারা পড়ে গেছে কাগজে, আর ভয় নেই। নিৰ্ভয়ে রেখে দিলেম, সে রাতের মত ছবির কাজ বন্ধ। জানলেম ছবি হয়ে গেছে, নির্ভাবনায় ঘরে গেলুম। সকালে উঠে ছবিতে শুধু দু-চারটে রঙের টান দেবার অপেক্ষা রইল।
এ রকম হয় শিল্পীর জীবনে, তবে সব ছবির বেলায় নয়।
তাই তো বলি ছবির জীবনে দুঃখ অনেক, আমিও চিরকাল সেই দুঃখই পেয়ে এসেছি। প্রাণে কেবলই একটা অতৃপ্তি থেকে যায়। কিছুতেই মনে হয় না যে, এইবারে ঠিক হল যেমনটি চেয়েছিলুম। কিন্তু তাই বলে থেমে গেলে চলবে না নিরুৎসাহ হয়ে পড়লে চলবে না। কাজ করে যাওয়াই হচ্ছে আমাদের কাজ। আবার কিছুকাল যদি ছবি না আসে তা হলেও মন খারাপ কোরো না। ছবি হচ্ছে বসন্তের হাওয়ার মতন। যখন বইবে তখন কোনো কথা শুনবে না। তখন একধার থেকে ছবি হতে শুরু হবে। মন খারাপ কোরো না—আমার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা মনে রেখো।
ছাত্রকে তার নিজের ছবি সম্বন্ধে মাস্টারের কিছু বাতলানো—এক-একসময়ে তার বিপদ বড়, আর তাতে মাস্টারেরও কি কম দায়িত্ব? একবার কি হয়েছিল বলি। নন্দলাল একখানা ছবি আঁকল ‘উমার তপস্যা’, বেশ বড় ছবিখানা। পাহাড়ের গায়ে দাঁড়িয়ে উমা শিবের জন্য তপস্যা করছে, পিছনে মাথার উপরে সরু চাঁদের রেখা। ছবিখানিতে রঙ বলতে কিছুই নেই, আগাগোড়া ছবিখানায় গৈরিক রঙের অল্প অল্প আভাস। আমি বললুম, ‘নন্দলাল, ছবিতে একটু রঙ দিলে না? প্রাণটা যেন চড়বড় করে ছবিখানির দিকে তাকালে। আর কিছু না দাও অন্তত উমাকে একটু সাজিয়ে দাও। কপালে একটু চন্দন-টন্দন পরাও, অন্তত একটি জবাফুল।’ বাড়ি এলুম, রাত্রে আর ঘুম হয় না। মাথায় কেবলই ঘুরতে লাগল, ‘আমি কেন নন্দলালকে বলতে গেলুম ও-কথা? আমার মতন করে নন্দলাল হয়তো উমাকে দেখেনি। ও হয়তো দেখেছিল উমার সেই রূপ, পাথরের মত দৃঢ়, তপস্যা করে করে রঙ রস সব চলে গেছে। তাই তো উমার তপস্যা দেখে তো বুক ফেটে যাবারই কথা। তখন আর সে চন্দন পরবে কি?’ ঘুমতে পারলুম না, ছটফট করছি কখন সকাল হবে। সকাল হতেই ছুটলুম নন্দলালের কাছে। ভয় হচ্ছিল পাছে সে রাত্রেই ছবিখানাতে রঙ লাগিয়ে থাকে আমার কথা শুনে। গিয়ে দেখি নন্দলাল ছবিখানাকে সামনে নিয়ে বসে রঙ দেবার আগে আর একবার ভেবে নিচ্ছে।
আমি বললুম, ‘কর কি নন্দলাল, থামো থামো, কি ভুলই আমি করতে যাচ্ছিলুম, তোমার উমা ঠিকই আছে। আর হাত লাগিয়ো না।’
নন্দলাল বললে, ‘আপনি বলে গেলেন উমাকে সাজাতে। সারারাত আমিও সে কথা ভেবেছি, এখনো ভাবছিলাম রঙ দেব কি না।’
কি সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলুম বল দেখি। আর একটু হলেই অত ভালো ছবিখানা নষ্ট করে দিয়েছিলুম আর কি। সেই থেকে খুব সাবধান হয়ে গেছি। আর এটা জেনেছি যে, ছবি যার যার নিজের নিজের সৃষ্টি, তাতে অন্য কেউ উপদেশ দেবে কি?
যখন আমাদের ভারতশিল্পের জোর চর্চা হচ্ছে তখন ভাবলুম যে, শুধু ছবিতে নয়, সব দিকেই এর চর্চা করতে হবে। লাগলুম আসবাবের দিকে, ঘর সাজাতে, আশেপাশে চারদিকে ভারতশিল্পের আবহাওয়া আনতে। ঘরে যত পুরোনো আসবাব ছিল কর্তাদের আমলের, বিদেশ থেকে আমদানি দামী দামী জিনিসপত্তর, সব বিক্রি করে দিলুম। বললুম, ‘সব ঝেড়ে ফেল্, যা কিছু আছে বাইরে ফেলে দে।’ মাদ্রাজী মিস্ত্রি ধনকোটি আচারি, তাকে এনে লাগিয়ে দিলুম কাজে। নিজে নমুনা দিই, নকশা দিই, আর তাকে দিয়ে আসবাব করাই। সব সাদাসিধে আসবাব করাই। তাকে দিয়ে ঘর জুড়ে জাপানী গদি করালুম। এই যে আজকাল তোমরা খাটের পায়া দেখছ, এ কোত্থেকে নেওয়া জানো? মাটির প্রদীপের দেল্খো থেকে। খেটেছি কম? প্রথম ভারতীয় আসবাবের চলন তো এইখান থেকেই হল। একলা আমি আর দাদা, এই আমাদের সব দিক সামলে চলতে হয়েছে; এখন এরা সবাই একটি ধারা পেয়ে গেছে। এ থেকে একটু আধটু নতুন কিছু এদিক ওদিক করতে পারা সহজ। কিন্তু আমাদের যে তখন গোড়াসুদ্ধ গাছ উপড়ে ফেলে নতুন গাছ লাগাতে হয়েছিল নিজের হাতে। চারা লাগানো থেকে জল ঢালা থেকে সবই আমাদেরই করতে হয়েছে। তাকে বাঁচিয়ে রেখেছি বলেই হয়তো তাতে একদিন ফুল ফোটাতে পারবে।
১৮. পুরীর পাণ্ডাঠাকুর
ছেলেবেলায় পুরীর পাণ্ডাঠাকুর আসত বাড়িতে, বছরে একবার। এলেই জগন্নাথ দেখবার ইচ্ছে জাগত মা পিসিমা ছেলেমেয়ে দাসী পাড়াপড়শি সকলেরই মনে। সে যে কি ঔৎসুক্য জগন্নাথ দেখবার। পাণ্ডাকে ঘিরে বলতে থাকতুম, ‘ও পাণ্ডাঠাকুর, কবে ঠাকুর দেখাবে বল না।’ দাসীরা একজন করে বেরিয়েও পড়ত তার সঙ্গে।
তার অনেক কাল পরে, বড় হয়েছি ছেলেপিলে নাতিনাতনি হয়েছে, রবিকা বাড়ি কিনলেন পুরীতে, বলুও কিনল, আমাদেরও বললেন জমি কিনতে। জগন্নাথ দেখবার ইচ্ছে মারও বরাবর। কিছু জমি কিনে নীলকুঠির একটা বাড়ি ভেঙে মশলাপাতি পাওয়া গেল খানিকটা, হাতেও টাকা এসে পড়ল কয়েক হাজার, তাই দিয়ে বাড়ি তৈরি হল পুরীতে, নাম হল ‘পাথারপুরী’।
তখনকার দিনে পুরী যাওয়া ছিল যেন মুসলমানের মক্কা যাওয়া। মা বউ ঝি ছেলেপুলে নিয়ে চললুম পুরীতে জগন্নাথ দৰ্শন করতে। কি উৎসাহ সকলের। মা সারারাত রইলেন জেগে বসে। আমরা শুয়ে আছি যে যার বেঞ্চিতে লম্বা হয়ে। কটক না কোন্ স্টেশনে উড়ে পালকিবেহারাদের ‘হুম্প হুয়া হুম্পা হুয়া’ কানে আসতেই মা বললেন, ‘ওঠ্, ওঠ্, এসে পড়েছি এবারে উড়েদের দেশে।’ ধড়মড় করে সব উঠে বসলুম। এমন মজা লাগল সে শব্দ শুনে, মনে হল যেন পুরীর জগন্নাথের সাড়া পাওয়া গেল, জগন্নাথের শব্দদূত। পালকির ‘হুম্পা হুয়া’য় বহুকাল আগে পাণ্ডাঠাকুরের শব্দ জ্যান্ত হয়ে আক্রমণ করলে। ট্রেন চলেছে হু হু করে, ভিতরে আমরা মুখ বাড়িয়ে আছি জানলা দিয়ে, কে আগে মন্দিরের চূড়ো দেখতে পাই। খানিক যেতে না-যেতেই ভোর হয়ে এল, দূরে দেখা দিল জগন্নাথের মন্দিরের চূড়া, দেখে কি আনন্দ। মনে হল এই রকম কি এর চেয়ে বেশি আনন্দই বুঝি পেয়েছিলেন চৈতন্যদেব, যদিও রেলে যাচ্ছি আমি। তার পর আর-এক আনন্দ সমুদ্র দেখার। স্টেশনের কাছেই বাড়ি, বাড়িতে এসেই তাড়াতাড়ি বারান্দায় গেলুম। দেখি কি চমৎকার নীল সেদিকটায়, চোখ জুড়িয়ে যায়, আর কি শব্দ, কি হাওয়া—যেন জগন্নাথের শাঁখ বাজছে।
দু-একদিনের মধ্যেই গুছিয়ে বসলুম। মা এক-এক করে সবাইকে পাঠিয়ে দিতে লাগলেন জগন্নাথদর্শনে। বাড়ির ছোট বড় দাসী চাকর কেউ বাদ নেই। আমিও তিন-চারদিন মন্দির ঘুরে দেখে এলুম সবকিছু। কেবল মাই বাকি। যাবার তেমন তাড়াই নেই। বলি, ‘পালকি ঠিক করে দিই, জগন্নাথ দৰ্শন করে আসুন।’ মা সে কথায় কানই দেন না—দিব্যি নিশ্চিন্ত, ভাবখানা যেন জগন্নাথ দর্শন হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে পালকি চড়ে সমুদ্রের ধারে খানিক হাওয়া খান, বেশির ভাগ বাড়িতেই বসে বসে ঘর সংসার খাওয়াদাওয়ার তদারক করেন আর সবাইকে ঠেলে ঠেলে মন্দিরে পাঠান।
একদিন হঠাৎ মা আমায় বললেন, ‘তুই জগন্নাথকে দেখেছিল?’
‘জগন্নাথ? না, তা তো দেখিনি।’
মা বললেন, ‘সে কি কথা! মন্দিরে গেলি অথচ বেদির উপরে ঠাকুর দেখলিনে? তোকে তা হলে জগন্নাথ দেখা দেননি, পাপ আছে তোর মনে, তাই।’
তা হবে। কতবার মন্দিরে গেছি—ঘুরে ঘুরে নিখুঁতভাবে সব কারুকাজ দেখেছি, কোথায় জগন্নাথের চন্দন বাটা হচ্ছে, কোথায় মালা গাঁথে, কোথায় ফুলের গয়না তৈরি করে মেয়েরা ব’সে, কোথায় সে সব ফুলের বাগান, কোথায় মাটির তলায় বটকৃষ্ণমূর্তি, সব দেখেছি। কিন্তু মা যখন ওই কথা বললেন তখন খেয়াল হল মন্দিরের ভিতরেও গেছি, অন্ধকারের মধ্যে প্রদীপের আলোতে ভিড় দেখেছি লোকজনের, কিন্তু জগন্নাথকে দেখিনি। আসলে আমি জগন্নাথকে দেখতে যাইনি; যা দেখতে গেছি তাই দেখেছি। যে যা দেখতে চায় তাই তো দেখতে পায়। মার কথা শুনে পরদিন আবার গেলুম মন্দিরে জগন্নাথকে দেখতে পাণ্ডা সঙ্গে নিয়ে, পাণ্ডাকে পাশে দাঁড় করিয়ে একেবারে ভিতরে গিয়ে জগন্নাথকে দেখে তাঁর সোনার চরণ স্পর্শ করে এলুম।
তখন মা বললেন, ‘এবারে আমায় দেখিয়ে আনতে পারিস?’
‘নিশ্চয়ই।’
পালকি ঠিক। পাণ্ডাকে বলে সব ব্যবস্থা করলুম যাতে না ভিড়ে মার কষ্ট হয়, বেশি না হাঁটতে হয়। বকশিশের লোভে সে ভিড় সরিয়ে ফাঁকা রাখল নাটমন্দির কিছুক্ষণের জন্য। তখন আমিই পাণ্ডা, যা বলছি তাই হচ্ছে। মাকে গরুড়স্তম্ভ, আনন্দবাজার, বৈকুণ্ঠ যা যা দেখবার সব এক-এক করে দেখিয়ে নিয়ে গেলুম ঠিক জগন্নাথের সামনে। অন্ধকারে ভয় পান এগতে, পড়ে যান বুঝিবা। বললুম, আমায় ধরুন ভাল করে; জগন্নাথের পা ছুঁয়ে আসবেন। পাণ্ডা পিদিম নিয়ে ‘বাবু উঁচা নিঁচা’ ‘উঁচা নিঁচা’ বলে, আর এক-এক সিঁড়ি নামে। এই করে করে বেদির কাছে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিলুম মাকে। জগন্নাথের পা ছোঁওয়া হল, এবারে প্রদক্ষিণ করতে হবে। প্রদক্ষিণ করা মানে অনেকখানি জায়গা ঘুরে আসা। অন্ধকারে আরসোলাগুলো ফড়ফড় করে উড়ছে, ভয় হতে লাগল মাকে নিয়ে এ কোথায় এলুম। যাক্, সব সেরে তো বাইরে এলুম। মা খুব খুশি। বারে বারে আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীৰ্বাদ করতে লাগলেন, ‘তোরই জন্য আমার জগন্নাথ দৰ্শন হল।’
উড্রফ, ব্লান্টও আসতেন, আমাদের বাড়িতেই উঠতেন এসে, কোনারকের ঝোঁক ছিল তাঁদের।
কত মজা করেছি পুরীতে শোভনলাল-মোহনলালদের নিয়ে। সেদিন ওদের জিজ্ঞেস করলুম, ‘সমুদ্র মনে আছে?’ বললে, ‘নেই।’ কি করে বা থাকবে, ওরা তখন কতটুকু-টুকু সব। ওদের নিয়ে সমুদ্রের পারে কাঁকড়া ধরতুম, কাঁকড়ার গর্তে রুটি ফেলে দিতুম। ঝোঁক গেল সমুদ্রে জাহাজ চালাতে হবে। ম্যানেজারকে লিখে খেলনার একটা বড় জাহাজ আনিয়ে তাতে সুতো বেঁধে পারে নাটাই হাতে আমি বসে রইলুম। চাকরকে বললুম জাহাজ নিয়ে জলে ছেড়ে দিতে। ইচ্ছে ছিল জাহাজ ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে যাবে, আমিও নাটাইয়ের সুতো খুলে দেব, পরে আবার টেনে তীরে আনব। কিন্তু সমুদ্রের সঙ্গে পরিচয় হতে দেরি হয়েছিল। চাকর হাঁটুজলে জাহাজ নিয়ে ছেড়ে দিলে। ওমা, এক ঢেউয়ে খেলার জাহাজ বালুতে বানচাল হয়ে গেল উলটে পড়ে। সমুদ্রে জাহাজ চালাবার শখ সেখানেই শেষ।
একদিন মোহনলাল বললে, ‘দেখ দেখ দাদামশায়, লাল চাঁদ উঠেছে?’ চেয়ে দেখি সূর্যোদয় হচ্ছে। মনে হয় একেবারে মাটি থেকে উঠছে যেন। বলি, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো, লাল চাঁদই তো বটে।’ আমারও অবস্থা তার মতই। সেদিন ছেলেমানুষের চোখে আমিও দেখলেম লাল চাঁদ।
বুড়ো ছাত্র জুটল এক সেখানে। বেশ তৈরি হয়ে গিয়েছিল কিছুকালের মধ্যেই। পরে পুরীতে আর্টের মাস্টার হয়ে চলে গেল। সাক্ষীগোপালে বাড়ি। একদিন বসে আছি, মাথায় একটা ঝুড়ি নিয়ে বুড়ো ছাত্র এল দুপুর রৌদ্রে। কি? না, ‘আম এনেছি আপনার জন্য।’
পাঁচ বছর উপরি-উপরি পুরীতে গিয়েছিলুম। সমুদ্রের হাওয়া যতদিন বইত, মা থাকতেন। উলটো দিকে হাওয়া বইতে থাকলেই মা চলে আসতেন; বলতেন, আর নয়।
একবার জ্যেঠামশায় এলেন পুরীতে, অসুখে ভুগে শরীর সারাতে। বাড়ির কাছেই বাড়ি ঠিক করে দিলেম, সঙ্গে কৃতী ভায়া, হেমলতা বোঠান ও মুনীশ্বর চাকর। জ্যেঠামশায় এসেছেন, গেলুম দেখা করতে। দেখি মুনীশ্বর দোতলার ছাদে একটা তক্তা তুলছে। কি ব্যাপার। জোঠামশায় বললেন, ‘এ কি রকম বাড়ি, আমি ভেবেছিলুম ঠিক সমুদ্রের উপরেই বাড়ি হবে—বসে বসে কেমন সুন্দর দেখব। কিন্তু এ তে তা নয়, কতখানি অবধি বালি, তার পর সমুদ্র।’ বললুম, ‘এইরকমই তো সকলের বাড়ি পুরীর সমুদ্রের ধারে। একেবারে বাড়ির তলা দিয়ে সমুদ্র বয়ে যাবে, তা কি করে হবে এখানে।’ জ্যেঠামশায়ের মন ভরে না বারান্দায় বসে সমুদ্র দেখে। দোতলার চিলঘরের সামনে একটা তক্তার উপরে কৌচ পেতে তার উপরে বসে সমুদ্র দেখে তবে খুশি। হেসে বলেন, ‘তোমাদের ওখান থেকে কি এইরকম দেখতে পাও?’ মাথা চুলকে বলি, ‘তা এইরকমই দেখতে বই কি খানিকটা।’
আত্মভোলা মানুষ ছিলেন জ্যেঠামশায়। একদিন বিকেলে বললেন, ‘চল সতুর বাড়িতে বেড়িয়ে আসি।’ সঙ্গে আমি ও কৃতী। খানিকক্ষণ গল্পসল্প করবার পর চুপচাপ বসে আছি সবাই। কিই বা আর বলবার থাকতে পারে। সন্ধ্যে হয়ে এল। আমরা উসখুস করছি। জ্যেঠামশায় দেখি নিৰ্বিকার হয়ে বসে আছেন, ওঠবার নামও নেই। ক্রমে রাত হয়ে এল, জ্যেঠামহাশয়ের খাবার সময় হল। হঠাৎ একসময়ে ‘মুনীশ্বর মুনীশ্বর’ বলে ডেকে উঠলেন। কৃতী বললে, ‘মুনীশ্বর তো এখানে আসেনি, সে তো বাড়িতে আছে।’ ‘ও, তাই বুঝি। এ বাড়ি তবে কার? আমি আরো ভাবছিলুম মুনীশ্বর আমায় খাবার দিচ্ছে না কেন, রাত হয়ে গেল। আচ্ছা ভুল হয়ে গিয়েছিল তো আমার।’ বলে হো হো করে হাসি।
মেজজ্যেঠামশায়ও এসেছিলেন পুরীতে সেবারে। আমরা তিনটে পরিবার পাশাপাশি। সুরেনও ছিল; জয়া, মঞ্জু ছোট ছোট। একদিন যা কাণ্ড। সুরেন চলেছে সমুদ্রের ধার দিয়ে ভিজে বালির উপরে। সঙ্গে জয়া মঞ্জু; সুরেনের সে খেয়াল নেই। এখন এক ঢেউয়ে নিয়েছে ভাসিয়ে জয়াকে। গেল গেল। সুরেন দেখে ঢেউয়ে চুল দেখা যাচ্ছে, টপ করে চুল ধরে টেনে তুললে মেয়েকে। কি সর্বনাশই হত আর একটু হলে।
কত বলব সেদেশের ঘটনা। পর পর কত কিছুই না মনে পড়ে—সে বিস্তর কথা। একবার আমি হারিয়ে গিয়েছিলুম সেও এক কাণ্ড। পুরীতে অনেক দিন আছি, ভেবেছি সব আমার নখদর্পণে। একদিন হাঁটতে হাঁটতে চক্ৰতীর্থ পেরিয়ে গেছি সমুদ্রের ধার দিয়ে, রাস্তা ছাড়িয়ে বালির উপর ধপাস ধপাস করে চলেইছি। কত দূর এসে পড়েছি কে জানে। হঠাৎ চটকা ভাঙল, দেখি সূর্যাস্ত হচ্ছে। যেদিকে চাই চতুর্দিকে ধু ধু বালি। না নজরে পড়ে জগন্নাথের মন্দির, না রাস্তা, না কিছু। শুধু শব্দ পাচ্ছি সমুদ্রের। কোন্ দিকে যাব ঘোর লেগে গেছে। তারা ধরে চলব, তারও তো কোনো জ্ঞান নেই। একেবারে স্তম্ভিত। শেষে সমুদ্রের শব্দ শুনে সেইদিকে চলতে লাগলুম। খানিক বাদে দেখি এক বুড়ি চলেছে লাঠি হাতে বললে, ‘কোথায় যাচ্ছ?’ বললুম, ‘চক্রতীর্থে।’ ভাবলুম চক্রতীর্থে পৌঁছতে পারলেই এখন যথেষ্ট। বুড়ি বললে, ‘তা যেদিকে যাচ্ছ সেদিকে সমুদ্র। আমার সঙ্গে এস, আমি যাচ্ছি চক্রতীর্থে।’ বুড়ির সঙ্গে চক্রতীর্থে ফিরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। নয়তো সারারাত সেদিন ঘুরে বেড়ালেও কিছু খুঁজে পেতুম না। ‘ভূতপত্রী’তে আছে এই বর্ণনা। অন্ধকারে সমুদ্রের ধারে বালির উপর হাঁটতে কেমন ভুতুড়ে মনে হয়—মনসাগাছগুলিও কেমন যেন।
সেইবারেই আমি ভূত দেখি। সত্যিই।
উড্রফ, ব্লাণ্ট কোনারক দেখে এসে বললেন, ‘যাও, দেখে এস আগে সে মন্দির।’ একদিন রওনা হলুম কোনারকে, চারখানা পালকিতে লাঠি লণ্ঠন লোকজন স্ত্রীপুত্রকন্যা সব সঙ্গে নিয়ে। ‘পথে বিপথে’ বইয়ে আছে এই বর্ণনা। কুড়ি মাইল পথ বালির উপর দিয়ে। যাচ্ছি তো যাচ্ছি, সারারাত। পান তামাক খাবার জলের কুঁজো পালকির ভিতরে তাকে ঠিক ধরা, মিষ্টান্নের ভাঁড়ও একটি, পাশে লাঠিখানা। পালকি চলেছে হুম্পাহুয়া। পুরী ছাড়িয়ে সারারাত চলেছি—ভয়ও হচ্ছে, কি জানি যদি বালির মাঝে পালকি ছেড়ে পালায় বেহারারা। আমার আগে আগে চলেছে তিনখানা পালকি; মাঝে মাঝে হাঁক দিচ্ছি, ‘ঠিক আছিস সবাই?’ সুনসান বালি, কোথায় যে আছি বাতাসে না পৃথিবীতে কিছু বোঝবার উপায় নেই। থেকে থেকে ধপাস ধপাস শব্দ, বেহারাদের আট-দশটা পা পড়ছে বালিতে। এক জায়গায় শুনি বাপ ঝপ ঝপ ঝপ শব্দ।
‘কি হল রে?’
‘বাবু, নিয়াখিয়া নদী আসি গেলাম।’
‘ও, আচ্ছা বেশ।’
নিয়াখিয়া নদী পেরিয়ে এলুম। শেষ রাত, চাঁদ অস্ত গেল, আবছা অন্ধকার, সকাল হতে আরো খানিকক্ষণ বাকি। সারারাত ভয়ে জেগে কাটিয়ে এলুম, এবারে একটু ঘুমও পাচ্ছে। সে সময়ে ভূতের ভয়ও একবার জেগেছিল মনে। সামনের পালকিগুলো আর দেখা যাচ্ছে না, বেহারাদের ডেকে বলি, ‘ও বেহারা, সব ঠিক আছে তো?’
‘সব ঠিক আছে বাবু, সব ঠিক আছে।’
এমন সময় দেখি, একটা লোক, একহাতে লাঠি একহাতে লণ্ঠন, চলেছে আমার পালকির খোলা দরজার পাশে পাশে।
বলি, ‘ও বেহারা, এ কে রে?’
‘আঃ বাবু, ওদিকে দেখো না, ওসব দেউতা আছে।’ বলে ওদিকের দরজা বন্ধ করে দিলে।
দেউতা বলে ওরা ভূতকে। বলি, ‘ওকি, লণ্ঠন হাতে দেউতা কি রে।’
খানিক বাদে দেখি ঘোড়ায় চড়ে একটা সাহেব টুপি মাথায় পাশ কাটিয়ে গেল।
‘বাবু, তুমি শুয়ে পড়।’ বলে শুধু বেহারারা।
শুনেছিলুম কোন্ এক মিলিটারিকে ওখানে মেরে ফেলেছিল, ভূত হয়ে সে ফেরে, অনেকেই দেখে।
রাত্তিরবেলা লণ্ঠন হাতে লোকটাকে দেখে আমার বরং ভালোই লেগেছিল।
যাক, এই করতে করতে এসে পৌঁছলুম সমুদ্রের ধারে কি একটা মন্দিরের কাছে, মেয়েরা সব নেমে দেখতে গেল। ছোট্ট একটি পাহাড়ের মতো, তার উপরে ছোট্ট মন্দিরটি। মণিলাল ছিল সঙ্গে, তাকে বললুম, ‘ঠিক আছ তো সবাই। এইবার তবে আমি একটু পাশ মোড় দিয়ে নিই।’ তারপর আমার পালকি পড়ল গিয়ে একেবারে কোনারকের ধারে। সিন্ধুতটে চলেছে পালকি হু হু করে। দরজা খুলে দেখলুম ঢেউগুলো পাড়ে এসে পড়ছে, আবার চলে যাচ্ছে পালকির নিচে দিয়ে। জলে ফসফরাস, ঢেউ আসে যায়, যেন একটা আলো চলে যায়। মনে হয় সমুদ্রের উপর দিয়ে ভেসে চলেছি, দানবরা কাঁধে করে নিয়ে চলেছে আমায়।
এইভাবে চলবার পর আবার একটা পালকি হু হু করে চলে গেল সামনে দিয়ে কোনারকের মন্দিরের দিকে, সঙ্গে আবার লণ্ঠন। ও কি, পালকি ওদিকে কোথায় গেল। নেমে দেখলুম আমাদের চারটে পালকি ঠিকই আছে। তবে ওটা কি?
বেহারারা ওই এক কথাই বলে, ‘দেখো না বাবু, তুমি শুয়ে পড়। কি দেখলুম তা হলে ওটা? মরীচিকা না কি কে জানে, তবে দেখেছিলুম ঠিকই। সকাল হয়ে গেছে, ভয় নেই। মণিলালদের জিজ্ঞেস করলুম, ‘দেখেছ কিছু?’
বললে, ‘না।’
ভূতুড়ে কাণ্ড দেখে কোনারকের মন্দিরে পৌছলুম। মেয়েরা নেমেই মন্দির দেখবে বলে ছুটল।
কোনারকের মত অমন সুন্দর সমুদ্র পুরীর নয়। গেলুম ধারে, আহা, যেন আছোঁয়া বালি সাদা জাজিমের মত বিছানো, তার কিনারায় নীল গভীর সমুদ্র। মানুষকে কাছে যেতে দেয় না। যেন বিরাট সভা, মানুষ সেখানে প্রবেশ করতে পারে না সহজে। তার ওদিকে সোনার ঘটের মত সূর্য উঠছে, সামনে সূর্যমন্দির। সূর্যোদয়ের আলোটা পড়ে এমন ভাবে, যেন সূর্যদেব উঠে এসে রথের শূন্য বেদি পূর্ণ করে বসবেন। সব তৈরি, এবার রথ চললেই হয়। বুঝেই ঠিক জায়গায় ঠিক রথটি নির্মাণ করেছিলেন শিল্পীরা।
মন্দিরও বড় ভালো লেগেছিল। কি তার কারুকাজ। ওই দেখেই তো বলেছিলেম ওকাকুরাকে, ‘যাও, সূর্যমন্দির দেখে এসো।’ মন্দিরের সামনে বালির উপরে পড়ে আছে একটি মূর্তি, আধখানা বালির নিচে পোঁতা—যেন পাষাণী অহল্যা পড়ে আছে মন্দিরের দুয়ারে। অহল্যা আঁকতে হলে ওই মূর্তিটি এঁকো।
সারাদিন কোনারকের মন্দির দেখে ডাকবাংলোতে থেকে বেলা কাটিয়ে বিকেল তিনটের সময় পালকি ছাড়লুম। আসছি আসছি। ফিরতি পথের শোভা, দূরে মৃগযূথ সব চলেছে—থেকে থেকে এক একবার দাঁড়ায় শিং তুলে, ঘাড় ফিরিয়ে। সে ছবি এঁকেছি। এই রকম চলতে চলতে আবার নিয়াখিয়া নদী পার হয়ে এলুম। সন্ধ্যে হয়ে এল, দেখলুম জগন্নাথের মন্দিরের ঠিক পিছনদিকে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। ঝপ করে পালকি নামিয়ে দিয়ে বেয়ারার জগন্নাথের মন্দির ছাড়িয়ে অনেক দূরে চূড়োর উপরে প্রকাশ পাচ্ছে যে সূর্য তারই দিকে তাকিয়ে দু-হাত জুড়ে প্রণাম করে বললে, ‘জয় মহাপ্রভু! জয় মহাপ্ৰভু!’
কিন্তু সত্যি বলব, এত সুন্দর সুন্দর মূর্তিগুলো দেখে লোভ হত। মনে হত রাবণের মত কোলে করে ঘরে নিয়ে যাই তাদের। সেই যে বালুর চরে আধখানা পোঁতা নায়িকা শুয়ে আছে আকাশের দিকে চেয়ে, দানবের শক্তি পেলে তুলে নিয়ে আসতুম।
একবার সত্যি সত্যিই মূর্তি চুরি করতে গিয়েওছিলুম। সংগ্রহের বাতিক চিরকালেরই তা তো জানো? সমুদ্রের ধারে পাথর পড়ে থাকে, যেতে আসতে দেখি, খেয়াল করিনে তেমন। একদিন নুলিয়াদের দিয়ে পাথরখানা ঘরে নিয়ে এলুম, দেখি তাতে ভৈরবী কাটা। মা বললেন, ‘এ ভালো নয়, কোনো ঠাকুর-টাকুর হবে। পুরীর মাটিও ঘরে নিয়ে যাওয়া দোষ। ও তুই ফিরিয়ে দে যেখানকার জিনিস সেখানে।’ পরে এক সাহেব নিয়ে গেল তা, আমার ভাগ্যে হল না। কি আর করি? মূর্তি ভাগ্যে নেই, নুড়িটুড়ি সংগ্রহ করে বেড়াই।
জগন্নাথের মন্দিরেও ঘুরি রোজ। নাটমন্দিরের ধারে ছোট্ট একটি ঘর, ছোট্ট দরজা, বন্ধই থাকে বেশির ভাগ। পাণ্ডা বললে, ভোগমূর্তি থাকে এখানে। জগন্নাথের বড় মূর্তি সব সময়ে নাড়াচাড়া করা যায় না, ওই মূর্তি দিয়েই কাজ চালায়। সে ঠিক ঘর নয়, একটি কুঠরি বললেই হয়। বললুম, ‘দেখতে চাই আমি।’ পাণ্ডা দরজা খুলে দিলে। দেখি চমৎকার চমৎকার ছোট্ট ছোট্ট মূর্তি সব। দেখেই লোভ হল। ছোট আছে, নিয়ে যাবারও সুবিধে। পাণ্ডাকে জিজ্ঞেস করলুম। সে বললে, ‘হবে না, ও হবে না বাবু।’ ফুসলে ফাসলে কিছু যখন হল না, দেখি তা হলে হাতানো যায় কিনা কিছু। ঘুরে ঘুরে সব জেনে শুনে সাহসও বেড়ে গেছে।
তখন স্নানযাত্রা। জগন্নাথকে নিয়ে রথ চলেছে, সবাই সেখানে, মন্দির খালি। আমার মন পড়ে আছে ছোট ছোট মূর্তিগুলোর উপর। আমি চুপি চুপি মন্দিরে ঢুকে সোজা উপস্থিত সেই পুতুলঠাসা কুঠরির কাছে, দেখি দরজা খোলা, ভিতর অন্ধকার। মস্ত সুবিধে, এবার চৌকাঠ পেরলেই হয়। আর দেরি নয়। দরজার কাছে গিয়ে উঁকি দিয়েছি কি অন্ধকার থেকে এক মূর্তি বলে উঠল, ‘কি বাবু, আপনি? আজ তো এখানে কিছু নেই, সব স্নানযাত্রায় চলে গেছে ।’ কি রকম থমকে গেলুম। ভিতরে যে কেউ বসে আছে একটুও টের পাইনি।
যাক, বাড়ি ফিরে এলুম ভাঙা মনে। সে রাত্রে স্বপ্ন দেখি, আমি যেন সেই কুঠরিতে ঢুকে একটা মূর্তি তুলে আনব ভেবে যেই তাতে হাত দিয়েছি মূর্তি হাত আর ছাড়ে না। চীৎকার করছি, ‘ওমা দেখ দেখ, হাত তুলে আনতে পারছিনে।’ দম বন্ধ হয়ে আসে স্বপ্নে। সকালে উঠে মাকে বললুম সব। মা বললেন, ‘খবরদার, কিছুতে হাত দিসনে, তবে সত্যিই হাত আটকে যাবে। সাবধান, ঠাকুরদেবতা নিয়ে কথা, আর কিছু নয়।’
কিন্তু কি বলব—এমন সুন্দর মূর্তি, তাকে চুরি করারও লোভ জাগায়।
তার পর আর-একদিন আর-একটা মূর্তি দেখলুম। নরেন্দ্রসরোবরের ধারে অনেক মূর্তি আছে, পাণ্ডারা ঘুরে ঘুরে দেখালে। তেমন কিছু নয়, পয়সা ফেলে ফেলে যাচ্ছি। একপাশে ছোট্ট একটা মন্দির, ভাঙা দরজা। বললুম, ‘এটাতে কি আছে দেখাও।’ পাণ্ডা বললে, ‘ওতে কিছু নেই, বাবু। ওটা এক বুড়ির মন্দির।’
বুড়িকে বললুম, ‘দেখা না বুড়ি তোর মন্দির।’ সে বললে, ‘দেখবে এসো।’ দরজাটি খুলে দেখাতেই একটি কালো কষ্টিপাথরের বংশীধারী মূর্তি, মানুষপ্রমাণ উঁচু, একটি হাত ভাঙা, যাকে বলে চিকনকালা বংশীধারী। কি তার সূক্ষ্ম কাজ, কি তার ভঙ্গি! কোথাও এমন দেখিনি। বুড়িকে বলেছিলুম, ‘মন্দির গড়িয়ে দেব, নতুন মূর্তি তৈরি করিয়ে দেব, এটি আমায় দে।’ রাজি হল না। নন্দলালদের বলেছিলুম, ‘যদি যাও, ভালো মূর্তি দেখতে চাও, সেটি দেখে এসো।’ এখনো সেই বুড়ি আছে কিনা, মূর্তি আছে কিনা কে জানে। পাণ্ডারা আমল দেয় না। বোধ হয় ভাঙা বলে ফেলে দিয়েছিল, বুড়ি তাকে পূজো করত। প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে গেল, কিন্তু ঘরে আনতে পারলেম না এই দুঃখ রইল।
তোমরা ‘ভারতশিল্প’‘ভারতশিল্প’ কর, দরদ কি আছে কারো? না পুরীর রাজার, না ম্যানেজারের, না পাণ্ডাদের, দরদ কারো নেই। প্রমাণ দিই।
জগন্নাথের মাসির বাড়ি মেরামত হবে। পাণ্ড খবর দিলে, ‘বাবু, দুটো হরিণ যদি কিনতে চাও মাসির বাড়ির, বিক্রি হবে।’
বললুম, ‘সে কি রে? পোষা হরিণ সেখানে বড় হয়েছে। আমার দরকার নেই সে হরিণের। ভাঙা মূর্তি থাকে তো বল্।
পাণ্ডা বললে, ‘সে কত চাই বাবু, বলুন। অনেক মিলবে।’
বললুম, ‘আজই চল্ তবে সেখানে দেখি গিয়ে।’
গেলুম, তখন সন্ধ্যেবেলা। সে গিয়ে যা দেখি। মাসির বাড়ি যেন ভূমিকম্পে উলটে পালটে গেছে। চুড়োর সিংহ পড়েছে ভুঁয়ে, পাতালের মধ্যে যে ভিত শিকড় গেড়ে দাঁড়িয়ে ছিল এতকাল সে শুয়ে পড়েছে মাটির উপরে, সব তছনছ। বড় বড় সিংহ নিয়ে কি করব? ছোটখাটাে মূর্তি পেলে নিয়ে আসা সহজ। ভিতরে গেলুম। সেখানেও তাই। এখানকার জিনিস ওখানে। কেমন একটা ত্রাস উপস্থিত হল। পাণ্ডাকে শুধালেম, এই পাথরের কাজ ঝেড়ে ঝুড়ে পরিষ্কার করে যেমন ছিল তেমনি করে তুলে দেওয়া হবে তো মেরামতের সময়?
তার কথার ভাবে বুঝলেম এই সব জগদ্দল পাথর ওঠায় যেখানকার সেখানে, এমন লোক নেই। বুঝলেম এ সংস্কার নয়, সৎকার। ভাঙা মন্দিরে মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে একজোড়া প্রকাণ্ড নীল হরিণ চার চোখে প্রকাণ্ড একটা বিস্ময় নিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এল। কতকালের পোষা হরিণ, এই মন্দিরের বাগানে জন্ম নিয়ে এতটুকু থেকে এত বড়টি হয়েছে—আজ এদের বিক্রি করা হবে। আর, এদের সঙ্গে সঙ্গে যে বাগান বড় হতে হতে প্রায় বন হয়ে উঠেছে, বনস্পতি যেখানে গভীর ছায়া দিচ্ছে, পাথি যেখানে গাইছে, হরিণ যেখানে খেলছে, সেই বনফুলের পরিমলে ভরা পুরোনো বাগানটা চষে ফেলে যাত্রীদের জন্য রন্ধনশালা বসানো হবে।
আমার যন্ত্রণাভোগের তখনও শেষ হয়নি। তাই ঘুরতে ঘুরতে একটা ডবল তালা দেওয়া ঘর দেখিয়ে বললেম, ‘এটাতে কি? পাণ্ডা আস্তে আস্তে ঘরটা খুললে, দেখলেম, মিণ্টন আর বর্ন্ কোম্পানির টালি দিয়ে অতবড় ঘরখানা ঠাসা।
‘এত টালি কেন?’
‘মাসির বাড়ি ছাওয়া হবে।’
আঃ সর্বনাশ, এরি নাম বুঝি মেরামত? ভাঙার মধ্যে, ধ্বংসের স্তূপে, রস আর রহস্য, নীল দুটি হরিণের মত বাসা বেঁধে ছিল। সেই যে শোভা, সেই শান্তি মনে ধরল না; ভালো ঠেকল দুখানা চকচকে রাঙা মাটির টালি!
ভাবলুম, এ ঠেকাতে হবে যে করেই হোক। সময় নেই, পরদিনই চলে আসছি কলকাতায়। বাড়ি ফিরে মণিলালের সঙ্গে পরামর্শ করে পুরীর কমিশনারের কাছে চিঠি লিখলুম।—‘আমি দেখে এসেছি এই কাণ্ড, ভ্যাণ্ডালিজ্মএর চূড়ান্ত। যে করে পারো তুমি থামিয়ো।’ ইংরেজ-বাচ্চা, যেমন চিঠি পাওয়া মাসির বাড়িতে নিজে গিয়ে হাজির। তখনি যেখানে যে পাথরটি ছিল তেমনি তুলিয়ে দিয়ে মেরামত করলে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে। কথা রাখলে সে। এই একটা পুণ্যকার্য করে এসেছি পুরীতে বলতে পার। জগন্নাথের মাসির বাড়ির শোভা নষ্ট হতে বসেছিল আর একটু হলেই।
সেবারেই নাচ দেখেছিলুম মন্দিরে দেবদাসীর। নাচ দেখা হয়নি, এ না দেখে যাওয়া হতে পারে না। নাচ আগে দেখি, পরে খাতায় সই দেব। পাণ্ডা কিছুতে ঘাড় পাতে না, বলে, ‘অনেক টাকা লাগবে।’ বললুম, ‘তা দেওয়া যাবে, সেজন্য আটকাবে না। দেবতার সামনে নাচ দেখব।’ সইয়ের লোভ, টাকার লোভ; পাণ্ডা রাজি হল অনেক গাঁইগুঁই করার পর। বললে, ‘কাল তবে খুব ভোরে এসে আপনাকে নিয়ে যাব। তৈরি থাকবেন।’
ভোরে আমি একলাই গেলুম তার সঙ্গে। তখনো মন্দিরে লোকজনের ভিড় হয়নি, অন্ধকারে দু-একটি মাথা দেখা যায় এখানে ওখানে, বোধ হয় পাণ্ডাদেরই। পাণ্ডা আমাকে নিয়ে নাটমন্দিরে বসিয়ে দিলে। একপাশে একটি মাদল বাজছে, একটি মশাল জ্বলছে, একটি দেবদাসী নাচছে। দেবদাসী নাচের সঙ্গে ঘুরছে ফিরছে, সঙ্গে সঙ্গে মশালও সেইদিকে ঘুরছে, আলো পড়ছে তার গায়, যেন জগন্নাথ দেখছেন তাকে আর কোণায় বসে দেখছি আমি। কত ভাব জানাচ্ছে দেবতার কাছে।
অভিনয়ে নটীর পূজা দেখে ছবি আঁকো তোমরা। আমি সত্যিসত্যিই দেবমন্দিরের ভিতরে গিয়ে দেবদাসীর নৃত্য দেখেছি। চমৎকার ব্যাপার সে। সেইবারেই ফিরে এসে দেবদাসীর ছবিখানি আঁকি। আর আঁকি কাজরী ছবিখানি। তাও দেখেছিলুম পুরীতেই কমিশনারের বাড়িতে। বাগানে পার্টি, মেঘলা আকাশ, টিপ টপ করে দু-একফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে, কয়েকটা বড় ফুলের গাছ, তার পাশে নাচছিল কয়েকটি ওড়িয়া মেয়ে। কাজরী ছবিখানি পরে তা থেকেই হল।
১৯. আরো কত যে দেখেছি
আরো কত যে দেখেছি, কত ছবি এঁকেছি, তার কি হিসেব আছে? না, আমিই তার হিসেব রেখেছি? আর, কি ভাবে কি থেকে যে ছবি এঁকেছি তা জানলে হিসেব চাইতে না আমার কাছে।
পুরীতে বসে সমুদ্র দেখেছি, নাচ দেখেছি; সেখানে আঁকিনি। বহুকাল পরে কলকাতায় বসে আঁকলুম সে সব ছবি।
মুসৌরিতে দেখেছি, ঘুরেছি। অনেককাল বাদে বের হল পাখির ছবিগুলি। সেখানে থাকতে ছবি আঁকিনি; ঘুরে ঘুরে দেখেছি, পাখির গান শুনেছি। পাখির গান সত্যিই আমায় আকর্ষণ করেছিল। শহরের পাখিগুলো গান গায় না, চেঁচায়—খাবার জন্যে চেঁচায়, বাসার জন্যে চেঁচায়, মারামারি করে চেঁচায়।
বলব কি মুসৌরি পাহাড়ের পাখিদের গানের কথা। উষাকাল, সূর্যোদয় দেখবার আশায় বসে আছি, কম্বল মুড়ি দিয়ে কান ঢেকে চুরুটটি ধরিয়ে খোলা পাথরের চাতালে ইজিচেয়ারে—সেই সময়ে আরম্ভ হল পাখিদের উষাকালের বৈতালিক। দূরের পাহাড়ে একটি পাখি একটু সুর ধরলে, সেখান থেকে আর-এক পাহাড়ে আর-একটি পাখি সে সুর ধরে নিলে। এমনি করতে করতে সমস্ত পাহাড়ে প্রভাতবন্দনা শুরু হয়ে গেল। তখনো সূর্যোদয় হয়নি। ধীরে ধীরে সামনের বরফের পাহাড়ের পিছনে সূর্য উঠছেন। সাদা বরফের চূড়ো দেখাচ্ছে ঘন নীল, যেন নীলমণির পাহাড়। পাখিদের বৈতালিক গান চলেছে তখনো। শেষ নেই—এ-পাহাড়ে, ও-পাহাড়ে, কত পাহাড়ে। যেমন সূর্য উদয় হলেন বৈতালিক গান থেমে গেল। সারাদিন আর গান শুনতেম না।
মানুষ জাগল। রিকশ চলল ঘণ্টা বাজিয়ে। টংটঙিয়ে কাজে চলল সবাই। দূরে মিশনরি স্কুলে ঘণ্টা বাজল, আকাশে ধ্বনি পাঠাতে লাগল টং টং টং টং। কাজের সুরে ভরে গেল অতবড় পাহাড়। এমনি সারাদিনের পর বেলাশেষে ছুটির ঘণ্টা বেজে উঠল স্কুলবাড়িতে, গির্জের ঘড়ি থামল প্রহর বাজিয়ে। সূর্য অস্ত গেলেন সমস্ত পাহাড়ের উপর ফাগের রঙ ছড়িয়ে দিয়ে। রাতের আকাশ ঘন নীল হয়ে এল—সন্ধ্যেতারা উঁকি দিলে কেলুগাছটার পাতার ফাঁকে। সেই সময়ে ধরলে দূর পাহাড়ে আবার বৈকালিক সুর, আরম্ভ হল পাখিদের গান আবার এ-পাহাড়ে ও-পাহাড়ে। একটি একটি করে সুর যেন ছুঁড়ে দিচ্ছে, লুফে লুফে নিচ্ছে পরস্পর। এমনি চলল কতক্ষণ। নীল আকাশের সীমা শুভ্র আলোয় ধুয়ে দিয়ে চন্দ্রও উঠলেন, পাখিরাও বন্ধ করলে তাদের বৈকালিক। সে যেন কিন্নরীদের গান, শুনে এসেছি রোজ দুবেলা।
গান তো নয়, যেন চন্দ্রসূর্যকে বন্দনা করত তারা। কোথায় লাগে তোমাদের সংগীত, সভার ওস্তাদি সংগীত। মন টলিয়েছিল কিন্নরীর দল। তাই বহুদিন পরে কলকাতায় তারাই সব এক-এক করে ফুটে বের হল আমার এক রাশ পাখির ছবিতে। দেখে নিয়ো, তার ভিতরে সুর আছে কিছু কিছু, যদিও মাটির রঙে সব সুর ধরা পড়েনি। সে কত পাখি, সব চোখেও দেখিনি, কানে শুনেছি তাদের গান।
মন কত ভাবে কত কি সংগ্রহ করে রাখে। সব যে বের হয় তাও নয় মনে হয়, হয়তো পূর্বজন্মেরও স্মৃতি থাকে কিছু। তাই তো ভাবি এক-একবার, লোকে যখন বলে পূর্বজন্মের কথা, উড়িয়ে দিতে পারিনে। নয়তো সারনাথে আমার ঘর খুঁজে পেলেম কি করে? দেখেই মনে হল এ আমার ঘর, এইখানে আমি থাকতুম, পুতুল গড়তুম, বেচতুম।
সে একবার পুরানো সারনাথ দেখতে গেছি। শুধু স্তূপটি আছে, মাটির নিচের শহর একটু একটু খুঁড়ে বের করছে সবে। তখন সন্ধ্যে হচ্ছে। বরুণা নদী, একটি সাদা বক ওপার থেকে এপারে ফিরে এল। বড় শান্তিপূর্ণ জায়গা। ঘুরে ঘুরে দেখছি। মাটির উপর ছোট একটি ঘর, আরো ছোট তার দরজা। দরজার চৌকাঠের উপর দুটি হাস আঁকা। চৌমাথা, কুয়ো সামনে একটি, যেন রাস্তার ধারের ঘরখানি। দেখেই মনে হল যেন আমার নিজের ঘর, কোনোকালে ছিলুম। এত তো দেখলুম, কোথাও এমন মনে হয়নি। ঠিক যেন নিজের বাড়ি বলে মনে হল। জোড়াসাঁকোর বাড়িতে ঢুকলে যেমন মনে হয়, ওই ঘরটির সামনে গিয়ে আমার হল তাই। নেলিকে বললুম, ‘ওরে দেখ্, দেখ্। এইখানে বসে আমি পুতুল গড়তুম; তারই দু-চারটে ওই যে পড়ে আছে এখনো।’ অলকের মা শুনে বললেন, ‘ও আবার কি সব বলছ, চল চল এখান থেকে।’
সব ছেড়ে ওই ঘরটার সামনে মন আমার থমকে দাঁড়াল, যেন মনের পরিচিত। অন্য সব চোখের উপর দিয়ে ভেসে গেল। তাই বলি, পূর্বজন্মের স্মৃতি থাকে হয়তো।
লোকে বলে, যে তারাকে দেখি চোখে সে তারা লোপ পেয়ে গেছে বহুযুগ আগে। তার আলোর কম্পনটুকুই দেখছি আমরা আজ তারারূপে। আমার মনও কি তাই। প্রাণের সেই বহুযুগ আগে লোপ পেয়ে যাওয়া কম্পন ধরে দিচ্ছে আজকের ছবিতে লোক-চোখের সামনে। আর্টিস্টের মনের হিসেব আর কাজের হিসেব ধরতে চাওয়া ভুল। ‘শাজাহানের মৃত্যুশয্যা,’ লোকে কেন বলে এত ঠিক হল কি করে? আমিও ভেবে পাইনে। কি জানি, কোনোকালে কি ছিলুম সেখানে। বুঝতে পারিনে। যেখানে থাকি, যার সঙ্গে উঠি বসি, বাস করি, তার ছবি আঁকা সহজ। কিন্তু যেখানে যাইনি, যা দেখিনি, সেখানকার এমন সঠিক ছবি আঁকতে কি করে পারলুম? এমনি হাজার ছবি, হাজার মুখ, মন ধরে রেখে দেয়। অনেক সময়ে আঁকি, বুঝতে পারিনে আমি আঁকছি কি আর কেউ আঁকাচ্ছে।
এখানে ঘুরে ফিরে সেই কথাই আসে—
কালি কলম মন
লেখে তিন জন।
এই তিন নইলে ছবি হয় না।
ওরে বাপু—
আঁখি যত জনে হেরে
সবারে কি মনে ধরে?
চোখ যত জিনিস দেখছে সে বড় কম নয়। কিন্তু সব কি আর মনে ধরছে। তা নয়। মনের মত যা তাই ধরছে, সেইগুলিই কাজে আসছে আমাদের ছবিতে। কত লোকজন, কত মুখ, অনেক সময় তারা চোখের উপর দিয়েই ভেসে যায়। সেইজন্যই বলে—
মনেরে না বুঝাইয়ে
নয়নেরে দোষো কেন?
চোখে মনে ঝগড়া।—মন বলে, ‘চোখ, তুমি ধরে রাখতে পারো না।’ চোখ বলে, ‘নিজের মনকে না বুঝে আমায় দোষো কেন।’
মন ধরে রাখে, দরকারমত বের করে নেয়। তাই তো বলি, শেষ ছবি আমার এখনো আঁকা হয়নি। আমারও কৌতুহল হয়, কি ছবি হবে সেটা। আঁকতে হবে, তার মানে মন ধাক্কা দিচ্ছে। আঁকা হলে বলব, এই হল সেই ছবি। তার পর বন্ধ। মন এখন দুয়োর খুলছে, দু-একটা বের করে দিচ্ছে। শুধু কি ছবি? দেখ, ছবি আছে, লেখা আছে, বাজনা ছিল, গলাও ছিল সাধা হয়নি। কিন্তু এই যে তিনটে চারটে আর্ট নিয়ে মনটা খেলা করছে, এখনো তার মধ্যে ছবিটা বেশি খেলা করছে। তবে দেখছি প্রত্যেকবার মন যেটা ধরে শেষ পর্যন্ত রস নিংড়ে তবে ছাড়ে, অক্টোপাসের মত। মন বড় ভয়ানক জানোয়ার। ওই অসুখের পর ডি. এন. রায় ডাক্তার বললেন আমায়, সব কাজ বন্ধ কর।’ মহামুশকিল। নিয়ে পড়লুম অণুবীক্ষণযন্ত্র। বসে বসে সব কিছু দেখি তা দিয়ে। বই পড়লুম, পোকামাকড় ঘাঁটলুম, নিজের হাতে প্লেট তৈরি করলুম, কত জানলুম।
মন ধরলে আর ছাড়তে চায় না। মোহনলালদের নিয়ে বসে দেখাতুম, তাদের পড়াতুম। সেই সময়ে এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখেছিলেম। ছোট্ট ছোট্ট এই এতটুকু সব কাঁকড়া পুষেছিলুম বিস্কুটের বাক্সে, সমুদ্রের জল-বালিও দিয়েছিলুম। কাঁকড়ারা নিজেরাই তাতে গর্ত করে বাসা তৈরি করে নিলে। রোজ সকালে সমুদ্রের ধারে কাঁকড়াদের যেমন রুটি খাওয়াই তেমনি তাদেরও খাওয়াই। একদিন একটু জ্যাম দিয়ে এক ফোঁটা রুটি ফেলে দিয়েছি কাঁকড়ার বাক্সে। কোত্থেকে একটা মাছি এরোপ্লেনের মত শোঁ করে বসল এসে জ্যাম-মাখানো রুটির টুকরোটির উপর। যেমন বসা, মাছিটার সমান হবে একটা কাঁকড়া দৌড়ে এসে আক্রমণ করলে মাছিটাকে। আমার হাতে অণুবীক্ষণযন্ত্র। দেখি মাছিতে কাঁকড়াতে ধ্বস্তাধস্তি লড়াই, যেন রাক্ষসে দানবে যুদ্ধ। কেউ কাউকে ছাড়ছে না। তখন বুঝলুম কি শক্তি ধরে দিয়েছে প্রকৃতি ওইটুকুরই মধ্যে। জার্মান-রাশিয়ান যুদ্ধের চেয়ে কম নয়। শেষে হার হল মাছিটারই। মনও ওই রকম, চোখে দেখিনে তাকে, কিন্তু ওই কাঁকড়ার মত ধরলে আর ছাড়বে না।
দেখলুম আর আঁকলুম, আমার ধাতে তা হয় না। অনেকদিন ধরে মনের ভিতরে যা তৈরি হল, তাই ছবিতে বের হল। মন ছিপ ফেলে বসে আছে চুপচাপ। আর সবই কি ঠিকঠাক বের হয়? মুসৌরি পাহাড়ের একটি সন্ধ্যের পাখি আঁকলুম, কি ভাবে সে ছবিটা এল?
সন্ধ্যে হচ্ছে, বসে আছি বারান্দায়, বাংলাদেশে সেদিন বিজয়া। হঠাৎ দেখি চেয়ে একটা লাল আলো পর পর পাহাড়গুলির উপর দিয়ে চলে গেল। সেই আলোয় পাহাড়ের উপরে ঘাসপাতা ঝিলমিল করে উঠল। মনে হল যেন ভগবতী আজ ফিরে গেলেন কৈলাসে, আঁচল থেকে খসা সোনার কুচি সব দিকে দিকে ছড়াতে ছড়াতে। রঙ, আলোর ঝিলমিল, তার সঙ্গে একটু ভাব—উমা ফিরে আসছেন কৈলাসে। তখনি ধরে রাখল মন। কলকাতায় এসে এই ছবি আঁকতে বসলুম। ঠিকঠাক সেইভাবেই কি বের হল ছবি? তা তো নয়, মনের কোণ থেকে বেরিয়ে এল সোনালি রূপোলি রং নিয়ে সুন্দরী একটি সন্ধ্যের পাখি—সে বাসায় ফিরছে। মনের এ কারখানা বুঝতে পারিনে। এত আলো, এত ভাব, সব তলিয়ে গিয়ে বের হল একটি পাখি, একটি কালে পাহাড়ের খণ্ড, আর তার গায়ে একগোছা সোনালি ঘাস। অনেক ছবিই আমার তাই—মনের তলা থেকে উঠে আসা বস্তু।
কবিকঙ্কণে এঁকেছি সব শেষের ছবি—দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে ঘট হাতে আসছে একটি মেয়ে। মুসৌরি পাহাড়ে বিজয়ার দিন ওই অমনি ছবির খসড়াই লিখেছিল মন, এও বুঝি তাই। সেই মুসৌরী পাহাড়ের কথা কতকাল বাদে বের হল কবিকঙ্কণে পটের ছবিতে।
ওইরকম কত ছবির তুমি হিসেব ধরবে? সব উলটাে পালটা। যেমন পুতুল গড়ি আর কি। আছে মানুষ, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে তাতে একদিন ঠোঁট বসিয়ে দিই, হয়ে যায় পাখি। তাই বলি চোখ আর মন এক জিনিস ধরে না সব সময়ে। মনই এখানে প্রবল। ইচ্ছে করলে চড়ুইপাখিকে স্বর্গের পাখি বানিয়ে দিতে পারে।
লেখাতেও তাই। চোখ দেখে ভায়োলেট ফুল, বাকিটা আসে কোত্থেকে? মন দেয় জোগান, চোখ ধরে পাত্রটা, মন ঢেলে দেয় তাতে মধু। তখন সে আর-এক জিনিস হয়ে যায়। তখনই হয় সোনার ময়ূর, সোনার হরিণ।
যাক আর্টের এসব তত্ত্বকথায় মাথা ঘামিয়ে কাজ নেই। এঁকে যাও, মন যোগ দেয় ভালো, নয়তো চোখের দেখাই যথেষ্ট।
চোখের দেখা দেখে আসি—
প্রাণের অধিক যারে ভালোবাসি।
প্রাণের অধিক ভালোবাসে বলেই তো চোখের দেখার এত দরকার।
২০. থেমেই তো গিয়েছিল সব
থেমেই তো গিয়েছিল সব। দশ-এগারো বছর ছবি আঁকিনি। আরব্য উপন্যাসের ছবির সেট আঁকা হলে ছেলেদের বললুম, ‘এই ধরে দিয়ে গেলুম। আমার জীবনের সব কিছু অভিজ্ঞতা এতেই পাবে।’ ব্যস্, তার পর থেকেই ছবি আঁকা বন্ধ। কি জানি, কেন মন বসত না ছবি আঁকতে। নতুন নতুন যাত্রার পালা লিখতুম; ছেলেদের নিয়ে যাত্রা করতুম, তাদের সাজাতুম, নিজে অধিকারী সাজতুম, ফুটাে ঢোল বাজাতুম, স্টেজ সাজাতুম। বেশ দিন যায়।
রবিকা বললেন, “অবন, তোমার হল কি? ছবি আঁকা ছাড়লে কেন?
বললুম, “কি জানো রবিকা, এখন যা ইচ্ছে করি তাই এঁকে ফেলতে পারি। সেজন্যই চিত্রকর্মে আর মন বসে না। নতুন খেলার জন্যে মন ব্যস্ত।’
এবার আবার এতকাল বাদে ছবি আঁকতে বসলুম। এ যেন নতুন সঙ্গী জুটিয়ে আর একবার পিছিয়ে গিয়ে পুরোনো রাস্তা মাড়ানোর মজা পাওয়া।
সবারই একটি করে জন্মতারা থাকে, আমারও আছে। সেই আমার জন্মতারার রশ্মি পৃথিবীর বুকে অন্ধকারে ছায়াপথ বেয়ে নেমে এসে পড়েছে অগাধ জলে। সেই দিন থেকে তার চলা শুরু হয়েছে।
তার পর একদিন চলতে চলতে, ঝিক ঝিক করতে করতে যখন এসে ঘাটে পৌঁছল, পৃথিবীর মাটিতে ম্লান আলো ঠেকল, সেখানে কি হল? না, সেখানে সেই আলো একটি নাম-রূপ পেলে, সেই আমি।
জন্মতারার আলো জীবননদী বেয়ে এসে তীরে ঠেকল। ওই ঘাটের ধারে দাড়িয়ে অবনীন্দ্রনাথ দেখলে—‘কোত্থেকে এলুম, এবারে কোথায় চলতে হবে।’
ঘাটে এসে ঠেকলুম, এবার চলা শুরু করতে হবে। মালবাহী গাধার মত, উদরের বোঝা পৃষ্ঠের বোঝা সব বোঝা নিয়ে জীবনের মুটে তখন চলেছে পথে, অতি ভীত ভাবে—কিছু দেখলেই ভয়ে পিছু হটে, তাকেও যে দেখে ভয়ে ছুটে পালায়। ঘাট ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল নানা জিনিস সংগ্রহ করতে হাটে, খানিকটা খেলার মত। অনেকদিন ধরে খেলার আয়োজন চলল। যেন সে একটি হারুয়া ছেলের মন, সে বাসায় ঢুকতে চাচ্ছে, গাছে চড়তে চাচ্ছে, ঠিক করতে পারছে না, চাঁদের মত উঁকিঝুঁকি মারছে গাছের আড়াল থেকে। ঘরের বুড়ি দাসী কোলে করে গায়—
ওই এক চাঁদ, এই এক চাঁদ
চাঁদে চাঁদে মেশামেশি।
এবারে খোঁজাখুজির পালা। কি নিয়ে খেলব? সঙ্গে আছে কে? ঘরের মানুষ বুড়ি দাসী। তার থেকেও জীবন রস টানছে। বাইরে থেকেও টানছে, ঘর থেকেও টানছে। যেমন ঘরের দাসী তেমনি পোষা পশুপাখি এরাও।
আস্তে আস্তে এল আশেপাশের সঙ্গে যোগাযোগ। বুনো ছাগল, খেলতে চাই তার সঙ্গে, সে চোখ রাঙিয়ে শিঙ বাগিয়ে তেড়ে আসে, অথচ মনকে টানে।
ফুলের ডাল দেখে মন চায় চড়ুইপাখি হয়ে তাতে ঝুলতে।
হাঁস উড়ে আসছে, এবারে মন আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে জানতে চায়। যেন মেঘদূতের যক্ষের মত পড়ে আছে একজন; সুদূরের আকাশ হতে সংবাদ নিয়ে এসে সামনে দিয়ে উড়ে গেল হাঁস।
এইকালে কল্পনা এল। গোল চাঁদ বেরিয়ে আসছে বনের ভিতর থেকে। মেঘ তাকে ঢেকে দিচ্ছে বারে বারে। ঘন বনে অদ্ভুত এক পাথি ডাকতে ডাকতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।
তার পর কত রকম সংগ্রহ, নানা ঘাটে ভিড়তে ভিড়তে চলেছে। কোথাও ফুল, কোথাও ছেলেমেয়ে কোথাও গাছ, কত কি! ঘাটে ঘাটে ঠেকেছে আর সংগ্রহ করেছে। বড় শৌখিন কাল সেটা। সে হচ্ছে রোমান্সের যুগ। স্ফূর্তি ক’রে, খেলায় মেতে, সময় কাটিয়ে শখের জিনিস সব সংগ্রহ করলে।
তার পর সংসার যেমনি চোখ রাঙালে, মহাকালের রক্তচক্ষু বললে, ‘কোথায় চলেছিস আনন্দে বয়ে? থাম্ এবারে।’ সেই মহাকালের ধমক খেয়ে মন চমকে উঠল। তখন আর খেলা-খেলনাতে মন বসে না। পুরোনো খেলনার বোঝা পিঠে বয়ে আর-এক ঘাটে চলল। ধমক খেয়ে এখন কোথায় যায়, কি করে, কি খেলে, এই ভাবনা।
জীবনতরু জল না পেলে বাঁচে না। পাথরের থেকেও রস নিতে চায়, যে পাষণের মঞ্চে সে বাঁধা থাকে তা থেকে।
তখন কে এল? তখন প্রভু এলেন তাকে বাঁচাবার জন্যে। বললেন, ‘সেই দিকে শিকড় পাঠা যেখান থেকে সে চিরদিন রস পাবে, বনবাসের আনন্দ পাবে।’
জোড়াগাছের স্মৃতি ঝাপসা হয়ে গেছে, ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে। অন্য গাছটিতে পড়েছে অস্তরবির আলে, তাপ দিয়ে বাঁচাতে চাচ্ছে। সবুজ মরে গিয়ে গৈরিক রঙের শোভা প্রকাশ পেল। সেখানে শুরু হল বনের ইতিহাস। অন্ধকার রাত্রে আর-এক সুর বাজল মনে। বনদেবীদের দেওয়া সেই স্বর।
সোনার স্বপ্ন যেন আর-একবার ধরা দেবে দেবে করলে, যেখানে সোনার হরিণ থাকে।
অলকার রঙছুট ময়ূরী এল। সে-জগতে সে রঙের অপেক্ষ রাখে না। সেই যে কুঞ্জে নূপুর বাজে সেখানে রঙছুট ময়ূরী খেলা করে। বিরহের গভীর সুর বাজে। মনময়ূরী একলা।
শক্ত পাথরে মন-পাখি বাধছে বাসা।
রঙছুট ছবি। ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে এল সবুজ রঙ। সেখানে ভোরের পাখি শীতের সকালে গান গেয়ে বলে, ‘বেরিয়ে আয় না আমার কাছে, রঙিন জগতে।’
স্মৃতি জাগায় বহুকাল আগের। মন চায় বাড়ি ফিরতে, বোঝা বাঁধাছাঁদা করে। স্বপ্নে দেখে বহুকাল আগের ছেড়ে-আসা বাড়ি ঘর ঘাট মাঠ গাছ।
তার পর সব শেষে প্রকৃতিমাতা দেখা দেন নিশাপরীর মত। নীল ডানায় ঢাকা আকাশ, ঘরের সন্ধ্যাপ্রদীপ ধরে একটুখানি আলো।
এই হল শিল্পীর জীবনের ধারার একটু ইতিহাস। শুধুই উজানভাটির খেলা। উজানের সময় সব কিছু সংগ্রহ করে চলতে চলতে ভাঁটার সময়ে ধীরে ধীরে তা ছড়িয়ে দিয়ে যাওয়া। বসন্তে যখন জোয়ার আসে ফুল ফুটিয়ে ভরে দেয় দিকবিদিক, আবার ভাঁটার সময়ে তা ঝরিয়ে দিয়ে যায়। আমারও যাবার সময়ে যা দুধারে ছড়িয়ে দিয়ে গেলুম তোমরা তা থেকে দেখতে পাবে, জানতে পাবে, কত ঘাটে ঠেকেছি, কত পথে চলেছি, কি সংগ্রহ করেছি ও সংগ্রহের শেষে নিজে কি বকশিশ পেয়ে গেছি।
এতকাল চলার পরে বকশিশ পেলুম আমি তিন রঙের তিন ফোটা মধু।