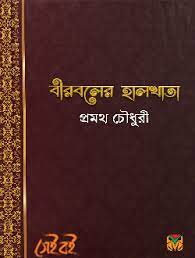- বইয়ের নামঃ বীরবলের হালখাতা
- লেখকের নামঃ প্রমথ চৌধুরী
- প্রকাশনাঃ সুচয়নী পাবলিশার্স
- বিভাগসমূহঃ গল্পের বই
আমরা ও তোমরা
আমরা ও তোমরা
তোমরা ও আমরা বিভিন্ন। কারণ তোমরা তোমরা, এবং আমরা আমরা। তা যদি না হত, তাহলে ইউরোপ ও এশিয়া এ দুই, দুই হত না–এক হত। আমি ও তুমির প্রভেদ থাকত না। আমরা ও তোমরা উভয়ে মিলে, হয় শুধু আমরা হতুম, নাহয় শুধু তোমরা হতে।
২.
আমরা পর্ব, তোমরা পশ্চিম। আমরা আরম্ভ, তোমরা শেষ। আমাদের দেশ মানবসভ্যতার সূতিকাগৃহ, তোমাদের দেশ মানবসভ্যতার শ্মশান। আমরা উষা, তোমরা গোধুলি। আমাদের অন্ধকার হতে উদয়, তোমাদের অন্ধকারের ভিতর বিলয়।
৩.
আমাদের রং কালো, তোমাদের রং শাদা। আমাদের বসন শাদা, তোমাদের বসন কালো। তোমরা শ্বেতাঙ্গ ঢেকে রাখো, আমরা কৃষ্ণদেহ খুলে রাখি। আমরা খাই শাদা জল, তোমরা খাও লাল পানি। আমাদের আকাশ আগন, তোমাদের আকাশ ধোঁয়া। নীল তোমাদের স্ত্রীলোকের চোখে, সোনা তোমাদের স্ত্রীলোকের মাথায়; নীল আমাদের শন্যে, সোনা আমাদের মাটির নীচে। তোমাদের ও আমাদের অনেক বর্ণভেদ। ভুলে যেন না যাই যে, তোমাদের দেশ ও আমাদের দেশের মধ্যে কালাপানির ব্যবধান। কালাপানি পার হলে আমাদের জাত যায়, না হলে তোমাদের জাত থাকে না।
৪.
তোমরা দৈর্ঘ্য, আমরা প্রস্থ। আমরা নিশ্চল, তোমরা চঞ্চল। আমরা ওজনে ভারি, তোমরা দামে চড়া। অপরকে বশীভূত করবার তোমাদের মতে একমাত্র উপায় গায়ের জোর, আমাদের মতে একমাত্র উপায় মনের নরম ভাব। তোমাদের পুরুষের হাতে ইস্পাত, আমাদের মেয়েদের হাতে লোহা। আমরা বাচাল, তোমরা বধির। আমাদের বুদ্ধি সক্ষম এত সক্ষম যে, আছে কি না বোঝা কঠিন; তোমাদের বুদ্ধি স্থূল–এত স্থূল যে, কতখানি আছে তা বোঝা কঠিন। আমাদের কাছে যা সত্য, তোমাদের কাছে তা কল্পনা; আর তোমাদের কাছে যা সত্য, আমাদের কাছে তা স্বপ্ন।
৫.
তোমরা বিদেশে ছটে বেড়াও, আমরা ঘরে শুয়ে থাকি। আমাদের সমাজ স্থাবর, তোমাদের সমাজ জঙ্গম। তোমাদের আদর্শ জানোয়ার, আমাদের আদর্শ উদ্ভিদ। তোমাদের নেশা মদ, আমাদের নেশা আফিং। তোমাদের সুখ ছটফটানিতে, আমাদের সখ ঝিমনিতে। সখ তোমাদের ideal, দুঃখ আমাদের real। তোমরা চাও দুনিয়াকে জয় করবার বল, আমরা চাই দুনিয়াকে ফাঁকি দেবার ছল। তোমাদের লক্ষ্য আরাম, আমাদের লক্ষ্য বিরাম। তোমাদের নীতির শেষ কথা শ্রম, আমাদের আশ্রম।
৬.
তোমাদের মেয়ে প্রায়-পুরুষ, আমাদের পুরুষ প্রায়-মেয়ে। বুড়ো হলেও তোমাদের ছেলেমি যায় না, ছেলেবেলাও আমরা বড়োমিতে পরিপূর্ণ। আমরা বিয়ে করি যৌবন না আসতে, তোমরা বিয়ে কর যৌবন গত হলে। তোমরা যখন সবে গৃহপ্রবেশ কর, আমরা তখন বনে যাই।
৭.
তোমাদের আগে ভালোবাসা পরে বিবাহ; আমাদের আগে বিবাহ পরে ভালোবাসা। আমাদের বিবাহ ‘হয়’, তোমরা বিবাহ ‘কর’। আমাদের ভাষায় মুখ্য ধাতু ‘ভূ’, তোমাদের ভাষায় ‘কৃ’। তোমাদের রমণীদের রূপের আদর আছে, আমাদের রমণীদের গুণের কদর নেই। তোমাদের স্বামীদের পাণ্ডিত্য চাই অর্থশাস্ত্রে, আমাদের স্বামীদের পাণ্ডিত্য চাই অলংকারশাস্ত্রে।
৮.
অর্থাৎ এককথায়, তোমরা যা চাও আমরা তা চাই নে, আমরা যা চাই তোমরা তা চাও না; তোমরা যা পাও আমরা তা পাই নে, আমরা যা পাই তোমরা তা পাও না। আমরা চাই এক, তোমরা চাও অনেক। আমরা একের বদলে পাই শুন্য, তোমরা অনেকের বদলে পাও একের পিঠে অনেক শন্য। তোমাদের দার্শনিক চায় যুক্তি, আমাদের দার্শনিক চায় মুক্তি। তোমরা চাও বাহির, আমরা চাই ভিতর। তোমাদের পুরুষের জীবন বাড়ির বাইরে, আমাদের পুরুষের মরণ বাড়ির ভিতর। আমাদের গান আমাদের বাজনা তোমাদের মতে শুধু বিলাপ, তোমাদের গান তোমাদের বাজনা আমাদের মতে শুধু প্রলাপ। তোমাদের বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য সব জেনে কিছু না জানা, আমাদের জ্ঞানের উদ্দেশ্য কিছু না জেনে সব জানা। তোমাদের পরলোক স্বর্গ, আমাদের ইহলোক নরক। কাজেই পরলোক তোমাদের গম্য, ইহলোক আমাদের ত্যাজ্য। তোমাদের ধর্মমতে আত্মা অনাদি নয় কিন্তু অনন্ত, আমাদের ধর্মমতে আত্মা অনাদি কিন্তু অনন্ত নয়— তার শেষ নির্বাণ। পবেই বলেছি, প্রাচী ও প্রতীচী পথক। আমরাও ভালো, তোমরাও ভালো শুধু তোমাদের ভালো আমাদের মন্দ ও আমাদের ভালো তোমাদের মন্দ। সুতরাং অতীতের আমরা ও বর্তমানের তোমরা, এই দুয়ে মিলে যে ভবিষ্যতের তারা হবে— তাও অসম্ভব।
শ্রাবণ ১৩০৯
ইতিমধ্যে
সম্পাদকমহাশয়েরা মধ্যেমধ্যে লেখকদের ‘ইতিমধ্যে’ একটা কিছু লিখে দিতে আদেশ করেন। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কি লিখব? তার উত্তরে বলেন, যাহোক-একটা-কিছু লেখো। কি যে লেখো তাতে কিছু আসে-যায় না–কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, লেখাটা ইতেমধ্যে হওয়া চাই। এথলে ইতিমধ্যের অর্থ হচ্ছে আগামী সংখ্যার কাগজ বেরবার পূর্বে। সম্পাদকমহাশয়েরা যখন আমাদের এইভাবে সাহিত্যের মাস্কাবার তৈরি করতে আদেশ দেন, তখন তাঁরা ভুলে যান যে, সাহিত্যে যারা পাকা, অঙ্গে তারা স্বভাবতই কাঁচা।
দিন গুণে কাজ করবার প্রবৃত্তিটি আমরা ইংরেজের কাছে শিখেছি। কোন দিনে কোন ক্ষণে কোন কার্য আরম্ভ করতে হবে, সেবিষয়ে এদেশে খুব বাঁধাবাধি নিয়ম ছিল; কিন্তু আরদ্ধ কর্ম কখন যে শেষ করতে হবে, সেসম্বন্ধে কোনোই নিয়ম ছিল না। সেকালে কোনো জিনিস যে তামাদি হত, তার প্রমাণ সংস্কৃত ব্যবহারশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। সেই কারণেই বোধ হয়, বহু মনোভাব ও আচারব্যবহার, যা বহুকাল পূর্বে তামাদি হওয়া উচিত ছিল, হিন্দুসমাজের উপর আজও তাদের দাবি পুরোমাত্রায় রয়েছে। সে যাই হোক, কাজের ওজনের সঙ্গে সময়ের মাপের যে একটু সম্বন্ধ থাকা উচিত— এ জ্ঞান আমাদের ছিল না। ‘কালোহয়ং নিরবধি’— এ কথা সত্য হলেও সেই কালকে মানুষের কর্মজীবনের উপযোগী করে নিতে হলে, তার যে ঘর কেটে নেওয়া আবশ্যক–এই সহজ সত্যটি আমরা আবিষ্কার করতে পারি নি। একটি নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর একটি বিশেষ কাজ শেষ করতে হলে প্রথমে কোথায় দাঁড়ি টানতে হবে, সেটি জানা চাই; তারপরে কোথায় কমা ও কোথায় সেমিকোলন দিতে হবে, তারও হিসেব থাকা চাই। এককথায়, সময়পদার্থটিকে punctuate করতে না শিখলে punctual হওয়া যায় না। সতরা আমরাও যে ইংরেজদের মত সময়কে টুকরো করে নিতে শিখছি, তাতে কাজের বিশেষ সুবিধে হবে; কিন্তু সাহিত্যের সুবিধে হবে কি না, সেবিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কারণ সময়ের মূল্যের জ্ঞান বড় বেশি বেড়ে গেলে সেই সময়ে যা করা যায় তার মুল্যের জ্ঞান, চাই কি, আমাদের কমেও যেতে পারে। জর্মান কবি গ্যেটে বলেছেন যে, মানুষের চরিত্র গঠিত হয় কর্মের ভিতর, আর মন গঠিত হয় অবসরের ভিতর। অর্থাৎ পেশী সবল করতে হলে মানুষের পক্ষে ছুটোছুটি করা দরকার, কিন্তু মস্তিষ্ক সবল করতে হলে মাথা ঠিক রাখা দরকার, স্থির থাকা দরকার। সাহিত্যরচনা করা হচ্ছে মস্তিষ্কের কাজ; সুতরাং ইতিমধ্যে’ বলতে যে অবসর বোঝায়, তার ভিতর সে রচনা করা সম্ভব কি না— তা আপনারাই বিবেচনা করবেন। তবে যদি কেউ বলেন যে, লেখার সঙ্গে মস্তিষ্কের সম্বন্ধ থাকাই চাই, এমন কোনো নিয়ম নেই, তাহলে অবশ্য গ্যেটের মতের মূল্য অনেকটা কমে আসে।
হাজার তাড়াহুড়ো করলেও লেখা-জিনিসটে যে কিঞ্চিৎ সময়সাপেক্ষ, তার প্রমাণ উদাহরণের সাহায্যে দেওয়া যেতে পারে। প্রথমে কবিতার কথা ধরা যাক। লোকের বিশ্বাস যে, কবিতার জন্মস্থান হচ্ছে কবির হৎপিণ্ড। তাহলেও হৃদয়ের সঙ্গে কলমের এমন-কোনো টেলিফোনের যোগাযোগ নেই, যার দরুন হৃদয়ের তারে কোনো কথা ধনিত হওয়ামাত্র কলমের মুখে তা প্রতিধ্বনিত হবে। আমার বিশ্বাস যে, যে-ভাব হৃদয়ে ফোটে, তাকে মস্তিষ্কের বক-যন্ত্রে না চুইয়ে নিলে কলমের মুখ দিয়ে তা ফোঁটা-ফোঁটা হয়ে পড়ে না। কলমের মুখ দিয়ে অনায়াসে মুক্ত হয় শুধু কালি, সাত রাজার ধন কালো মানিক নয়। অতএব কবিতা রচনা করতেও সময় চাই। তারপর ছোট গল্প। মাসিকপত্রের উপযোগী গল্প লিখতে হলে প্রথমে কোনো-না-কোনো ইংরেজি বই কিংবা মাসিকপত্র পড়া চাই। তারপর সেই পঠিত গল্পকে বাংলায় গঠিত করতে হলে তাকে রপান্তরিত ও ভাষান্তরিত করা চাই। এর জন্যে বোধ হয় মূলগল্প লেখবার চাইতেও বেশি সময়ের আবশ্যক।
কিছুদিন পূর্বে ভারতবর্ষের অতীত সম্বন্ধে যা-খুশি-তাই লেখবার একটা সুবিধে ছিল। একালে এদেশে কিছুই নেই, অতএব সেকালে এদেশে সব ছিল’— এইকথাটা নানারকম ভাষায় ফলিয়ে-ফেনিয়ে লিখলে সমাজে তা ইতিহাস বলে গ্রাহ্য হত। কিন্তু সে সুযোগ আমরা হারিয়েছি। একালে ইতিহাস কিংবা প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে লিখতে হলে তার জন্য এক-লাইব্রেরি বই পড়াও যথেষ্ট নয়। প্রত্নরত্ন এখন মাটি খুঁড়ে বার করতে হয়, সুতরাং ইতিমধ্যে’, অর্থাৎ সম্পাদকীয় আদেশের তারিখ এবং সামনে-মাসের পয়লার মধ্যে, সে কাজ করা যায় না। অবশ্য ম্যালেরিয়ার বিষয় কিছুই না জেনে অনেক কথা লেখা যায় কিন্তু সে লেখা সাহিত্য-পদবাচ্য কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। যার একপাশে ভ্রমরগঞ্জন আর অপরপাশে মধ, তাই আমরা সাহিত্য বলে স্বীকার করি। দুঃখের বিষয়, ম্যালেরিয়ার একপাশে মশকগুঞ্জন আর অপরপাশে কুইনীন। সুতরাং সাহিত্যেও ম্যালেরিয়া হতে দরে থাকাই শ্রেয়। বিনা চিন্তায়, বিনা পরিশ্রমে, আজকাল শুধু দুটি বিষয়ের আলোচনা করা চলে; এক হচ্ছে উন্নতিশীল রাজনীতি, আর-এক হচ্ছে স্থিতিশীল সমাজনীতি। কিন্তু এ দুটি বিষয়ের আলোচনা সচরাচর সভাসমিতিতেই হয়ে থাকে। অতএব ও দুই হচ্ছে বক্তাদের একচেটে। লেখকেরা যদি বক্তাদের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করেন, তাহলে বক্তারাও লিখতে শুরু করবেন, এবং সেটা উচিত কাজ হবে না।
লেখবার নানারূপ বিষয় এইভাবে ক্রমে বাদ পড়ে গেলে শেষে একটিমাত্র জিনিসে গিয়ে ঠেকে, যার বিষয় নির্ভাবনায় অনর্গল লেখনী চালনা করা চলে, এবং সে হচ্ছে নীতি। নীতির মোটা আদেশ ও উপদেশগুলি সংখ্যায় এত কম যে, তা আলে গোনা যায়, এবং সেগুলি এতই সর্বলোকবিদিত ও সর্ববাদিসম্মত যে, সখশরীরে স্বচ্ছন্দচিত্তে সেবিষয়ে এক-গগা লিখে যাওয়া যায়; কেননা, কেউ যে তার প্রতিবাদ করবে, সে ভয় নেই।
মানুষ যে দেবতা নয়, এবং মানবের পক্ষে দেবত্বলাভের চেষ্টা নিত্য ব্যর্থ হলেও যে নিয়ত কর্তব্য, সেবিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। তবুও অপরকে নীতির উপদেশ দিতে আমার তাদশ উৎসাহ হয় না। তার কারণ, মানুষ খারাপ বলে আমি দুঃখ করি নে, কিন্তু মানুষ দুঃখী বলে মন খারাপ করি। অথচ মানুষের দুর্গতির চাইতে দুর্নীতিটি বেশি চোখে না পড়লে নীতির গরগিরি করা চলে না।
তাছাড়া পরের কানে নীতির মন্ত্র দেওয়া সম্বন্ধে আমার মনে একটি সহজ অপ্রবত্তি আছে। যেকথা সকলে জানে, সেকথা যে আমি না বললে দেশের দৈন্য ঘুচবে না, এমন বিবাস আমি মনে পোষণ করতে পারি নে। এমনকি আমার এ সন্দেহও আছে যে, যাঁরা দিন নেই রাত নেই অপরকে লক্ষ্মীছেলে হতে বলেন, তাঁরা নিজে চান শুধু লক্ষ্মীমন্ত হতে। যাঁরা পরকে বলেন তোমরা ভালো হও, ভালো কর’, তাঁরা নিজেকে বলেন ‘ভালো খাও, ভালো পর’। সুতরাং আমার পরামর্শ যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে আমি তাঁকে বলব ‘ভালো খাও, ভালো পর। কারণ মানুষে পৃথিবীতে কেন আসে কেন যায়, সে রহস্য আমরা না জানলেও এটি জানি যে ‘ইতিমধ্যে তার পক্ষে খাওয়া-পরাটা দরকার।
‘তোমরা ভালো খাও, ভালো পর’, এ পরামর্শ সমাজকে দিতে অনেকে কুণ্ঠিত হবেন; কেননা, ওকথার ভিতর এইকথাটি উহ্য থেকে যায় যে, পরামর্শদাতাকে নিজে ভালো হতে হবে এবং ভালো করতে হবে। আপত্তি তো ঐখানেই।
যিনি ভালো খান ও ভালো পরেন, সহজেই তাঁর মনে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের উপর বিশ্বাস জন্মে যায়, এবং সেইসঙ্গে এই ধারণাও তাঁর মনে দঢ় হয়ে ওঠে যে, যেখানে দৈন্য সেইখানেই পাপ।
দারিদ্র্যের মূলে যে দরিদ্রের দুর্নীতি, এই ধারণা একসময়ে ইউরোপের ধনীলোকের মনে এমনি বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল যে, এই ভুলের উপর ‘পোলিটিকাল ইকনমি’-নামে একটি উপবিজ্ঞান বেজায় মাথাঝাড়া দিয়ে উঠেছিল। অর্থ যে ধর্মমূলক, এর প্রমাণ পৃথিবীতে এতই কম যে, আমাদের পর্বপুরুষেরা একটি পর্বজন্ম কল্পনা করে সেই পর্বজন্মের পাপপণ্যের ফলস্বরূপ সুখদুঃখ সমাজকে মেনে নিতে শিখিয়েছিলেন।
ব্যাখ্যার চাতুর্যে জিৎ অবশ্য আমাদের পূর্বপুরুষদেরই, কারণ বহু লোকের দুঃখকষ্ট যে তাদের ইহজন্মের কর্মফলে নয়, তা প্রমাণ করা যেতে পারে; কিন্তু সে যে পর্বজন্মের কমফলে নয়, তা এ জন্মে অপ্রমাণ করা যেতে পারে না।
আসলে দুইজনের মুখে একই কথা। সে হচ্ছে এই যে, পরের দুঃখ যখন তাদের নিজের দোষে, তখন তাদের শুধু ভালো হতে শেখাও, তাদের দুঃখ দর করার চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য নয়। অতএব মানুষের দুর্গতির প্রতি করণ হওয়া উচিত নয়, তাদের দুর্নীতির প্রতি কঠোর হওয়াই কর্তব্য।
কিন্তু আজকাল কালের গুণে শিক্ষার গুণে আমরা পরের দুঃখ সম্বন্ধে অতটা উদাসীন হতে পারি নে, কর্মফলে আস্থা রেখে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি নে। তাই দীনকে নীতিকথা শোনানো অনেকে হীনতার পরিচায়ক মনে করেন। ছোটছেলে সম্বন্ধে পড়লে-শুনলে দুধ-ভাতু’, এ সত্যের পরিবর্তে ‘আগে দুধভাত, পরে পড়াশনো’, এই সত্যের প্রচার করতে চাই। এদেশের দভিক্ষ-প্রপীড়িত জনগণের জন্য আমরা শিক্ষার ব্যবস্থা করবার পূর্বে অন্নের ব্যবস্থা করা শ্রেয় মনে করি। আগে অন্নপ্রাশন, পরে বিদ্যারল্ড–সংস্কারেরও এই সনাতন ব্যবস্থা বজায় রাখা আমাদের মধ্যে সংগত। অথচ আমরা যে কেন ঠিক উলটো পদ্ধতির পক্ষপাতী, তার অবশ্য কারণ আছে।
লোকশিক্ষার নামে যে আমরা উত্তেজিত হয়ে উঠি, তার প্রথম কারণ যে আমরা শিক্ষিত। স্কুলে লিখে এসে যে-কালি আমরা হাত আর মুখে মেখেছি, তার ভাগ আমরা দেশসদ্ধ লোককে দিতে চাই। যেমনি একজনে লোকশিক্ষার সুর ধরেন অমনি আমরা যে তার ধুয়ো ধরি, তার আর-একটি কারণ এই যে, এ কাজে আমাদের শুধু বাক্যব্যয় করতে হয়, অর্থ ব্যয় করতে হয় না। এ ব্যাপারে লাগে লাখ টাকা, দেবে গৌরসরকার।
জনসাধারণের হাতে-খড়ি দেবার পরিবর্তে মুখে-ভাত দেবার প্রস্তাবে আমরা যে তেমন গা করি নে তার কারণ, সাংসারিক হিসাবে সকলের স্বার্থসাধন করতে গেলে নিজের স্বার্থ কিঞ্চিৎ খর্ব করা চাই; ত্যাগস্বীকারের জন্য নীতি নিজে শেখা দরকার, পরকে শেখানো দরকার নয়।
আমাদের প্রত্যেকের নিজের স্বার্থ যে সমগ্র জাতির স্বার্থের সহিত জড়িত, এ জ্ঞান যে আমাদের হয়েছে তার প্রমাণ বাংলাসাহিত্যের কতকগুলি নতুন কথায় পাওয়া যায়। ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের কথা, জাতীয় আত্মজ্ঞানের কথা, আজকাল বক্তাদের ও লেখকদের প্রধান সম্বল। অথচ একথাও অস্বীকার করবার জো নেই যে, এত বলা-কওয়া সত্ত্বেও এই অঙ্গাঙ্গী ভাব পরস্পরের গলাগলি ভাবে পরিণত হয় নি; আর জাতীয় আত্মজ্ঞান শুধু জাতীয় অহংকারে পরিণত হচ্ছে, যদিচ অহংজ্ঞানই আত্মজ্ঞানের প্রধান শত্র। জাতীয় কত ব্যবৃদ্ধি অনেকের মনে জাগ্রত হলেও জাতীয় কর্তব্য যে সকলে করেন না, তার কারণ, পরের জন্য কিছু করবার দিন আমরা নিত্যই পিছিয়ে দিই। আমাদের অনেকের চেষ্টা হচ্ছে–প্রথমে নিজের জন্য সব করা, পরে অপরের জন্য কিছু করা। সুতরাং জাতীয় কর্তব্যটকু আর ইতিমধ্যে করা হয় না। ফলে আপনি বাঁচলে বাপের নাম’, এই পুরনো কথার উপর আমরা নিজের কর্মজীবন প্রতিষ্ঠা করি, আর ‘জাত বাঁচলে ছেলের নাম’, এইরকম একটা কোনো বিশ্বাসের বলে জাতীয় কর্তব্যের ভারটা, এখন যারা ছেলে এবং পরে যারা মানুষ হবে, তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিই।
কিন্তু আসল কথা হচ্ছে যে, যা-কিছু করতে হবে, তা ইতিমধ্যেই করতে হবে। সম্পাদকমহাশয়েরা, লেখক নয়, পাঠকদের যদি এই সত্যটি উপলব্ধি করাতে পারেন, তাহলে তাঁদের সকল অজ্ঞা আমরা পালন করতে প্রস্তুত আছি।
জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
কথার কথা
সম্প্রতি বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে আমাদের ক্ষুদ্র সাহিত্যসমাজে একটা বড়রকম বিবাদের সূত্রপাত হয়েছে। আমি বৈয়াকরণ নই, হবারও কোনো ইচ্ছে নেই। আলেকজান্দ্রিয়ার বিখ্যাত লাইব্রেরি মুসলমানরা ভস্মসাৎ করেছে বলে সাধারণত লোকে দুঃখ করে থাকে, কিন্তু প্রসিদ্ধ ফরাসি লেখক মনটেইনের মনোভাব এই যে, ও ছাই গেছে বাঁচা গেছে! কেননা, সেখানে অভিধান ও ব্যাকরণের এক লক্ষ গ্রন্থ ছিল। বাবা! শুধু কথার উপর এত কথা! আমিও মনটেইনের মতে সায় দিই। যেহেতু আমি ব্যাকরণের কোনো ধার ধারি নে, সুতরাং কোনো ঋষিঋণমুক্ত হবার জন্য এ বিচারে আমার যোগ দেবার কোনো আবশ্যক ছিল না। কিন্তু তর্ক-জিনিসটে আমাদের দেশে তরল পদার্থ, দেখতে-না-দেখতে বিষয় হতে বিষয়ান্তরে অবলীলাক্রমে গড়িয়ে যাওয়াটাই তার স্বভাব। তর্কটা শুরু হয়েছিল ব্যাকরণ নিয়ে, এখন মাঝামাঝি অবস্থায় অলংকারশাস্ত্রে এসে পৌঁছেছে, শেষ হবে বোধ হয় বৈরাগ্যে। সে যাই হোক, পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় এই মত প্রচার করেছেন যে, আমরা লেখায় যত অধিক সংস্কৃত শব্দ আমদানি করব ততই আমাদের সাহিত্যের মঙ্গল। আমার ইচ্ছে, বাংলাসাহিত্য বাংলাভাষাতেই লেখা হয়। দুর্বলের স্বভাব, নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না। বাইরের একটা আশ্রয় আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়। আমরা নিজের উন্নতির জন্যে পরের উপর নির্ভর করি। স্বদেশের উন্নতির জন্যে আমরা বিদেশীর মুখাপেক্ষী হয়ে রয়েছি, এবং একই কারণে নিজভাষার শ্রীবৃদ্ধির জন্যে অপর ভাষার সাহায্য ভিক্ষা করি। অপর ভাষা যতই শ্রেষ্ঠ হোক-না কেন, তার অঞ্চল ধরে বেড়ানোটা কি মনুষ্যত্বের পরিচয় দেয়? আমি বলি, আমরা নিজেকে একবার পরীক্ষা করে দেখি না কেন। ফল কি হবে, কেউ বলতে পারে না; কারণ কোনো সন্দেহ নেই যে, সে পরীক্ষা আমরা পূর্বে কখনো করি নি। যাক ওসব বাজে কথা। আমি বাংলাভাষা ভালোবাসি, সংস্কৃতকে ভক্তি করি। কিন্তু এ শাস্ত্র মানি নে যে, যাকে শ্রদ্ধা করি তারই শ্রাদ্ধ করতে হবে। আমার মত ঠিক কিংবা শাস্ত্রীমহাশয়ের মত ঠিক, সে বিচার আমি করতে বসি নি। শুধু তিনি যে যুক্তিদ্বারা নিজের মত সমর্থন করতে উদ্যত হয়েছেন, তাই আমি যাচিয়ে দেখতে চাই।
২.
কেউ হয়ত প্রথমেই জিজ্ঞাসা করতে পারেন, বাংলাভাষা কাকে বলে। বাঙালির মুখে এ প্রশ্ন শোভা পায় না। এ প্রশ্নের সহজ উত্তর কি এই নয় যে, যে ভাষা আমরা সকলে জানি শুনি বুঝি, যে ভাষায় আমরা ভাবনাচিন্তা সুখদুঃখ বিনা আয়াসে বিনা ক্লেশে বহুকাল হতে প্রকাশ করে আসছি, এবং সম্ভবত আরও বহুকাল পর্যন্ত প্রকাশ করব, সেই ভাষাই বাংলাভাষা? বাংলাভাষার অস্তিত্ব প্রকৃতিবাদ অভিধানের ভিতর নয়, বাঙালির মুখে। কিন্তু অনেকে, দেখতে পাই, এই অতি সহজ কথাটা স্বীকার করতে নিতান্ত কুণ্ঠিত। শুনতে পাই কোনো-কোনো শাস্ত্রজ্ঞ মৌলবি বলে থাকেন যে, দিল্লির বাদশাহ, যখন উর্দভাষা সৃষ্টি করতে বসলেন, তখন তাঁর অভিপ্রায় ছিল একেবারে খাঁটি ফারসিভাষা তৈয়ারি করা, কিন্তু বেচারা হিন্দুদের কান্নাকাটিতে কৃপাপরবশ হয়ে হিন্দিভাষার কতকগুলো কথা উর্দুতে ঢুকতে দিয়েছিলেন। আমাদের মধ্যেও হয়ত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদের বিশ্বাস যে, আদিশূরের আদিপুরুষ যখন গৌড়ভাষা সৃষ্টি করতে উদ্যত হলেন, তখন তাঁর সংকল্প ছিল যে ভাষাটাকে বিলকুল সংস্কৃতভাষা করে তোলেন, শুধু গৌড়বাসীদের প্রতি পরম অনুকম্পাবশত তাদের ভাষার গুটিকতক কথা বাংলাভাষায় ব্যবহার করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। এখন যাঁরা সংস্কৃতবহুল ভাষা ব্যবহার করবার পক্ষপাতী, তাঁরা ঐ যে গোড়ায়-গলদ হয়েছিল তাই শুধুরে নেবার জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়েছেন। আমাদের ভাষায় অনেক অবিকৃত সংস্কৃত শব্দ আছে, সেইগুলিকেই ভাষার গোড়াপত্তন ধরে নিয়ে, তার উপর যত পার আরও সংস্কৃত শব্দ চাপাও–কালক্রমে বাংলায় ও সংস্কৃতে দ্বৈতভাব থাকবে না; আসলে আমীলোকের কাছে এখনো নেই। মাতৃভাষার মায়ায় বদ্ধ বলে আমরা সংস্কৃত-বাংলায় অদ্বৈতবাদী হয়ে উঠতে পারছি নে। বাংলায় ফারসি কথার সংখ্যাও বড় কম নয়, ভাগ্যক্রমে ফারসিপড়া বাঙালির সংখ্যা বড় কম। নইলে সম্ভবত তাঁরা বলতেন, বাংলাকে ফারসিবল করে তোলে। মধ্যে থেকে আমাদের মা-সরস্বতী কাশী যাই কি মক্কা যাই, এই ভেবে আকুল হতেন। এক-একবার মনে হয় ও উভয়সংকট ছিল ভালো, কারণ একেবারে পণ্ডিত মণ্ডলীর হাতে পড়ে মা’র আশু কাশীপ্রাপ্তি হবারই অধিক সম্ভাবনা।
৩.
এই প্রসঙ্গে পণ্ডিতপ্রবর সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের প্রথম বক্তব্য এই যে, সাহিত্যের উৎপত্তি মানুষের অমর হবার ইচ্ছায়। যা-কিছু বর্তমান আছে, তার কুলজি লিখতে গেলেই গোড়র দিকটে গোঁজামিলন দিয়ে সারতে হয়। বড় বড় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক, যথা শংকর স্পেন্সার প্রভৃতিও, ঐ উপায় অবলম্বন করেছেন। সুতরাং কোনো জিনিসের উৎপত্তির মূল নির্ণয় করতে যাওয়াটা বৃথা পরিশ্রম। কিন্তু একথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, আর যা হতেই হোক অমর হবার ইচ্ছে থেকে সাহিত্যের উৎপত্তি হয় নি। প্রথমত, অমরত্বের ঝকি আমরা সকলে সামলাতে পারি নে, কিন্তু কলম চালাবার জন্য আমাদের অনেকেরই আঙুল নিসপিস করে। যদি ভালো-মন্দ-মাঝারি আমাদের প্রতি কথা, প্রতি কাজ চিরস্থায়ী হবার তিলমাত্র সম্ভাবনা থাকত, তাহলে মনে করে দেখুন তো আমরা ক’জনে মুখ খুলতে কিংবা হাত তুলতে সাহসী হতুম। অমরত্বের বিভীষিকা চোখের উপর থাকলে, আমরা যা perfect তা ব্যতীত কিছু বলতে কিংবা করতে রাজি হতুম না। আর আমরা সকলেই মনে মনে জানি যে, আমাদের অতি ভালো কাজ, অতি ভালো কথাও perfectionএর অনেক নীচে। আসল কথা, মৃত্যু আছে বলেই বেচে সখ। পণ্যক্ষয় হবার পর আবার মত লোকে ফিরে আসবার সম্ভাবনা আছে বলেই দেবতারা অমরপুরীতে ফর্তিতে বাস করেন, তা না হলে স্বর্গও তাঁদের অসহ্য হত। সে যাই হোক, আমরা মানুষ, দেবতা নই; সুতরাং আমাদের মুখের কথা দৈববাণী হবে, এ ইচ্ছা আমাদের মনে স্বাভাবিক নয়।
দ্বিতীয়ত, যদি কেউ শুধু অমর হবার জন্য লিখব, এই কঠিন পণ করে বসেন, তাহলে সে ইচ্ছা সফল হবার আশা কত কম বুঝতে পারলে তিনি যদি বুদ্ধিমান হন তাহলে লেখা হতে নিশ্চয়ই নিবত্ত হবেন। কারণ সকলেই জানি যে হাজারে ন-শ-নিরানব্বই জনের সরস্বতী মতবৎসা। তাছাড়া সাহিত্যজগতে মড়ক অষ্টপ্রহর লেগে রয়েছে। লাখে এক বাঁচে, বাদবাকির প্রাণ দু দণ্ডের জন্যও নয়। চরক পরামর্শ দিয়েছেন, যেদেশে মহামারীর প্রকোপ সেদেশ ছেড়ে পলায়ন করাই কর্তব্য। অমর হবার ইচ্ছায় ও আশায়, কে সে রাজ্যে প্রবেশ করতে চায়?
৪.
বিদ্যাভূষণমহাশয়ের আরও বক্তব্য এই যে, জীয়ন্ত ভাষার ব্যাকরণ করতে নেই, তাহলেই নির্ঘাত মরণ। সংস্কৃত মৃতভাষা, কারণ ব্যাকরণের নাগপাশে বন্ধ হয়ে সংস্কৃত প্রাণত্যাগ করেছে। আরও বক্তব্য এই যে, মুখের ভাষার ব্যাকরণ নেই, কিন্তু লিখিত ভাষার ব্যাকরণ নইলে চলে না। প্রমাণ, সংস্কৃত শুধু অমরত্ব লাভ করেছে, পালি প্রভৃতি প্রাকৃতভাষা একেবারে চিরকালের জন্য মরে গেছে। অর্থাৎ, এককথায় বলতে গেলে, যে-কোনো ভাষারই হোক না কেন, চিরকালের জন্য বাঁচতে হলে আগে মরা দরকার। তাই যদি হয়, তাহলে বাংলা যদি ব্যাকরণের দড়ি গলায় দিয়ে আত্মহত্যা করতে চায়, তাতে বিদ্যাভূষণমহাশয়ের আপত্তি কি। তাঁর মতানুসারে তো যমের দুয়োর দিয়ে অমরপুরীতে ঢুকতে হয়। তিনি আরও বলেন যে, পালি প্রভৃতি প্রাকৃতভাষায় হাজার হাজার গ্রন্থ রচিত হয়েছে, কিন্তু প্রাকৃত সংস্কৃত নয় বলে পালি প্রভৃতি ভাষা লুপ্ত হয়ে গেছে। অতএব, বাংলা যতটা সংস্কৃতের কাছাকাছি নিয়ে আসতে পার, ততই তার মঙ্গল। যদি বিদ্যাভূষণমহাশয়ের মত সত্য হয়, তাহলে সংস্কৃতবহুল বাংলায় লেখা কেন, একেবারে সংস্কৃতভাষাতেই তো আমাদের লেখা কর্তব্য। কারণ, তাহলে অমর হবার বিষয় আর কোনো সন্দেহ থাকে না। কিন্তু একটা কথা আমি ভালো বুঝতে পারছি নে : পালি প্রভৃতি ভাষা মত সত্য, কিন্তু সংস্কৃতও কি মত নয়? ও দেবভাষা অমর হতে পারে, কিন্তু ইহলোকে নয়। এ সংসারে মৃত্যুর হাত কেউ এড়াতে পারে না; পালিও পারে নি, সংস্কৃতও পারে নি, আমাদের মাতৃভাষাও পারবে না। তবে যে-কদিন বেচে আছে, সে-কদিন সংস্কৃতের মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে বেড়াতে হবে, বাংলার উপর এ কঠিন পরিশ্রমের বিধান কেন। বাংলার প্রাণ একটুখানি, অতখানি চাপ সইবে না।
৫.
এবিষয়ে শাস্ত্রীমহাশয়ের বক্তব্য যদি ভুল না বুঝে থাকি, তাহলে তাঁর মত সংক্ষেপে এই দাঁড়ায় যে, বাংলাকে প্রায় সংস্কৃত করে আনলে আসামি হিন্দুস্থানি প্রভৃতি বিদেশী লোকদের পক্ষে বঙ্গভাষাশিক্ষাটা অতি সহজসাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠবে। দ্বিতীয়ত, অন্য ভাষার যে সুবিধাটুকু নেই, বাংলার তা আছে— যে-কোনো সংস্কৃত কথা যেখানে হোক লেখায় বসিয়ে দিলে বাংলাভাষার বাংলাত্ব নষ্ট হয় না। অর্থাৎ যাঁরা আমাদের ভাষা জানেন না, তাঁরা যাতে সহজে বুঝতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে, সাধারণ বাঙালির পক্ষে আমাদের লিখিত ভাষা দবোধ করে তুলতে হবে। কথাটা এতই অদ্ভুত যে, এর কি উত্তর দেব ভেবে পাওয়া যায় না। সুতরাং তাঁর অপর মতটি ঠিক কি না দেখা যাক। আমাদের দেশে ছোটছেলেদের বিশ্বাস যে, বাংলা কথার পিছনে অনুঘর জুড়ে দিলে সংস্কৃত হয়; অরি প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের মত যে, সংস্কৃত কথার অনস্বর বিসর্গ ছেটে দিলেই বাংলা হয়। দুটো বিশ্বাসই সমান সত্য। বাঁদরের ল্যাজ কেটে দিলেই কি মানুষ হয়? শাস্ত্রীমহাশয় উদাহরণস্বরূপে বলেছেন, হিন্দিতে ‘ঘরমে যায়গা’ চলে, কিন্তু ‘গৃহমে যায়গা’ চলে না— ওটা ভুল হিন্দি হয়। কিন্তু বাংলায় ঘরের বদলে গৃহ যেখানে-সেখানে ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ, সকল ভাষার একটা নিয়ম আছে, শুধু বাংলাভাষার নেই। যার যা-খুশি লিখতে পারি, ভাষা বাংলা হতেই বাধ্য। বাংলাভাষার প্রধান গুণ যে, বাঙালি কথায় লেখায় যথেচ্ছাচারী হতে পারে। শাস্ত্রীমহাশয়ের নির্বাচিত কথা দিয়েই তাঁর ও ভুল ভাঙিয়ে দেওয়া যায়। ‘ঘরের ছেলে ঘরে যাও, ঘরের ভাত বেশি করে খেয়ো’, এই বাক্যটি হতে কোথাও ‘ঘর’ তুলে দিয়ে ‘গৃহ’ স্থাপনা করে দেখুন তো কানেই বা কেমন শোনায়, আর মানেই বা কত পরিষ্কার হয়।
৬.
আসল কথাটা কি এই নয় যে, লিখিত ভাষায় আর মুখের ভাষায় মূলে কোনো প্রভেদ নেই? ভাষা দুয়েরই এক, শুধু প্রকাশের উপায় ভিন্ন–একদিকে স্বরের সাহায্যে, অপরদিকে অক্ষরের সাহায্যে। বাণীর বসতি রসনায়। শুধু মুখের কথাই জীবন্ত। যতদূর পারা যায়, যে ভাষায় কথা কই সেই ভাষায় লিখতে পারলেই লেখা প্রাণ পায়। আমাদের প্রধান চেষ্টার বিষয় হওয়া উচিত কথায় ও লেখায় ঐক্য রক্ষা করা, ঐক্য নষ্ট করা নয়। ভাষা মানুষের মুখ হতে কলমের মুখে আসে, কলমের মুখ হতে মানুষের মুখে নয়। উলটোটা চেষ্টা করতে গেলে মুখে শুধু কালি পড়ে। কেউ-কেউ বলেন যে, আমাদের ভাবের ঐশ্বর্য এতটা বেড়ে গেছে যে বাপ-ঠাকুরদাদার ভাষার ভিতর তা আর ধরে রাখা যায় না। কথাটা ঠিক হতে পারে, কিন্তু বাংলাসাহিত্যে তার বড়-একটা প্রমাণ পাওয়া যায় না। কণাদের মতে ‘অভাব’ একটা পদার্থ। আমি হিন্দুসন্তান, কাজেই আমাকে বৈশেষিক-দর্শন মানতে হয়। সেই কারণেই আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, প্রচলিত বাংলাসাহিত্যেও অনেকটা পদার্থ আছে। ইংরেজিসাহিত্যের ভাব, সংস্কৃতভাষার শব্দ, ও বাংলাভাষার ব্যাকরণ–এই তিন চিজ, মিলিয়ে যে খিচুড়ি তয়ের করি, তাকেই আমরা বাংলাসাহিত্য বলে থাকি; বলা বাহুল্য, ইংরেজি না জানলে তার ভাব বোঝা যায় না। আমার এক-এক সময়ে সন্দেহ হয় যে, হয়ত বিদেশের ভাব ও পরোকালের ভাষা, এই দুয়ের আওতার ভিতর পড়ে বাংলাসাহিত্য ফুটে উঠতে পারছে না। একথা আমি অবশ্য মানি যে, আমাদের ভাষায় কতক পরিমাণে নতুন কথা আনবার দরকার আছে। যার জীবন আছে, তারই প্রতিদিন খোরাক যোগাতে হবে। আর আমাদের ভাষার দেহপষ্টি করতে হলে প্রধানত অমরকোষ থেকেই নতুন কথা টেনে আনতে হবে। কিন্তু যিনি নূতন সংস্কৃত কথা ব্যবহার করবেন, তাঁর এইটি মনে রাখা উচিত যে, তাঁর আবার নূতন করে প্রতি কথাটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করতে হবে; তা যদি না পারেন তাহলে বঙ্গ-সরস্বতীর কানে শুধু পরের সোনা পরানো হবে। বিচার না করে একরাশ সংস্কৃত শব্দ জড়ো করলেই ভাষারও শ্রীবৃদ্ধি হবে না, সাহিত্যেরও গৌরব বাড়বে না, মনোভাবও পরিষ্কার করে ব্যক্ত করা হবে না। ভাষার এখন শানিয়ে বার বার করা আবশ্যক, ভার বাড়ানো নয়। যেকথাটা নিতান্ত না হলে নয়, সেটি যেখান থেকে পার নিয়ে এস, যদি নিজের ভাষার ভিতর তাকে খাপ খাওয়াতে পার। কিন্তু তার বেশি ভিক্ষে ধার কিংবা চুরি করে এনো না। ভগবান পবননন্দন বিশল্যকরণী আনতে গিয়ে আস্ত গন্ধমাদন যে সমূলে উৎপাটন করে এনেছিলেন, তাতে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দেন নি।
জ্যৈষ্ঠ ১৩০১
কনগ্রেসের আইডিয়াল
১৮৮৫ খৃস্টাব্দে বোম্বাই-বন্দরে কনগ্রেসের জন্ম হয়। ১৯০৬ খস্টাব্দে কলিকাতা-শহরে তা সাবালক হয়। তার পরবৎসর সুরাট-নগরীতে তার মৃত্যু হয়। এ বৎসর আবার তার জন্মস্থানে তার পুনর্জন্ম হয়েছে।
এবার কিন্তু কনগ্রেসের ধড়ে প্রাণ আসে নি, তার প্রাণে ধড় এসেছে। সকলেই জানেন, সুরাটে কনগ্রেসের মৃত্যু হয় নি, তার অপমৃত্যু ঘটেছিল; আর সে যেমন-তেমন অপমৃত্যু নয়— একসঙ্গে খুন এবং আত্মহত্যা। এদেশে কারও অপমৃত্যু ঘটলে তার আত্মার ততদিন সদগতি হয় না, যতদিন-না তা আবার একটি নূতন দেহে প্রবেশ লাভ করতে পারে। কনগ্রেসের সক্ষম শরীর তাই এ কয় বৎসর একটি স্থূল শরীরের তল্লাসে এদেশে-ওদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, অতঃপর বোম্বাই-ধামে তা লাভ করেছে। গত কনগ্রেসে বিশ হাজার লোক জমায়েত হয়েছিল।
কনগ্রেসওয়ালাদের মতে কিন্তু কনগ্রেসের কস্মিনকালেও মৃত্যু হয় নি। সুরাটে শুধু স্বরাট পাগল হয়ে কনগ্রেসকে জখম করে নিজে করেছিলেন আত্মহত্যা। তার পর, যেহেতু সে ধরাট কনগ্রেসেই জন্মলাভ করেছিল, সেইজন্য তার ভূত তার জন্মদাতার স্কন্ধে ভর করবার চেষ্টায় ফিরছিল। সেই ভূতের ভয়ে কনগ্রেস এতদিন ঘরের দুয়োর বন্ধ করে বসেছিল। এই বন্ধ ঘরের দূষিত বায়তেই তার শরীর কাহিল হয়ে গিয়েছিল। অথচ কনগ্রেস এই ভূতের উপদ্রব থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোনো উপায় বার করতে পারে নি। এবার নবমন্ত্রের বলে স্বরাটের ভূত, ভবিষ্যৎ হয়ে গেছে। তাই কনগ্রেসের দেহটি আবার নাদুশনুদুশ হয়ে উঠেছে। এককথায় কনগ্রেস এবার বেচে ওঠে নি, বেঁচে গিয়েছে।
সে যাই হোক। কনগ্রেসের এবার ভোল ফিরেছে এবং সেইসঙ্গে তার বোল ফিরেছে। এতদিন কনগ্রেস ছিল বড়দিনের দুর্গোৎসব; তিনদিন ধরে ‘ধনং দেহি মানং দেহি’ বলে দু’সন্ধ্যা ইংরেজিতে মন্ত্র আওড়ানো এবং সেই উপলক্ষ্যে খানা-পিনা নাচ-তামাশা আমোদ-আহ্লাদ, এবং তার পরে বিসর্জন, এবং তার পরে কনগ্রেসওয়ালাদের পরস্পর-কোলাকুলি করে গৃহাভিমুখে যাত্রা–এই ছিল কনগ্রেসের হাল ও চাল।
ভবিষ্যতে শুনছি কনগ্রেসের সপ্তমী অষ্টমী নবমী থাকবে, কিন্তু দশমীতেই সব শেষ হবে না। তার পর বারোমাস ধরে কনগ্রেস তার স্বধর্ম প্রচার করবে। অর্থাৎ কনগ্রেস এবার জাতীয়-রাজনৈতিক-শিক্ষা-পরিষদে পরিণত হল। কনগ্রেসের এ সংকল্প অতি সাধ সংকল্প সন্দেহ নেই; কিন্তু যেবিষয়ে সন্দেহ আছে তা হচ্ছে এই যে, এ সংকল্প কার্যে পরিণত হবে কি না।
প্রথমত রাজনীতি বলতে যা বোঝায়, তা দেশসুদ্ধ লোককে বোঝানো কঠিন। ও-পদার্থ আমরা ইউরোপ থেকে আমদানি করেছি। সেদেশে একালে ও-বস্তু হচ্ছে তাই, যার ভিতর একদিক দিয়ে দেখতে গেলে রাজাও নেই, নীতিও নেই; আবার আর-একদিক দিয়ে দেখতে গেলে, ও-দুইই আছে। এই দুটো দিক যাতে একসঙ্গে চোখে পড়ে, এমন করে দেশের চোখ-ফোটানোর জন্য যে জ্ঞানাঞ্জনশলাকার আবশ্যক, তা দেশীভাষা নয়। ব্রহন যে একাধারে সগুণ এবং নির্গুণ, এ সত্য বোঝাতে হলে যেমন সংস্কৃতভাষার সাহায্য চাই— তেমনি রাজনীতি যে একসঙ্গে রাজমন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্র হতে পারে, এ সত্য বোঝাতে হলে ইংরেজির সাহায্য চাই।
কনগ্রেস অবশ্য এতে পিছপাও হবে না। কেননা, কনগ্রেসের পাণ্ডারা ঐ এক ইংরেজিভাষাই জানেন, এবং ঐ এক ইংরেজিভাষাই মানেন। তবে তাঁদের কথা বোঝে, এমন লোক দেশে ক’টি। অতএব তাঁরা যদি দেশকে রাজনৈতিক-শিক্ষা দিতে বসেন তো ফলে দাঁড়াবে এই যে, কনগ্রেসওয়ালারাই পালা করে পরস্পর-পরস্পরের গরশিষ্য হবেন। সুতরাং যতদিন-না ভারতবর্ষের ত্রিশ কোটি লোক ইংরেজি-শিক্ষিত হয়ে ওঠে, ততদিন এই রাজনৈতিক-শিক্ষার কাটা মুলতবি রাখাই কর্তব্য। সে শিক্ষা যে শুধু নিষ্ফল হবে তাই নয়, তার কুফলও হতে পারে। শিক্ষা দিতে গিয়ে হয়ত কনগ্রেসকে দু দিন পরে দেশের লোককে বলতে হবে— ‘উলটা বুঝিলি রাম। এ বিপদ যে আছে, তার প্রমাণও আছে। আর এরূপ উলটা বোঝাটা রামের পক্ষে আরামের নয়। এবং সে অবস্থায় কনগ্রেসের পক্ষে তাকে ভ্যাবাগঙ্গারাম বলাটাও সংগত নয়।
দ্বিতীয়ত, জাতীয় রাজনৈতিক শিক্ষার জন্য একটা জাতীয় রাজনৈতিক আদর্শ থাকা আবশ্যক। একটা আইডিয়াল যে থাকা চাইই চাই, একথা কনগ্রেসও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে। এস্থলে যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, কন,গ্রেস কি আজও তেমন-কোনো রাজনৈতিক আদর্শের সন্ধান পেয়েছেন? তাহলে কনগ্রেসওয়ালারা উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিবেন, অবশ্য পেয়েছি। এবং সে আদর্শের নাম হচ্ছে, ‘সাম্রাজ্যের ভিতর ঘরাজ্য।
নিত্য দেখতে পাই যে, এক দলের মতে ভারতবর্ষে ধরাজকতার অর্থ হচ্ছে অরাজকতা, আর-এক দলের মতে অরাজকতার অর্থই হচ্ছে স্বরাজকতা। এই দুটি হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক-গগনের শুক্ল আর কৃষ্ণ পক্ষ। কনগ্রেস অবশ্য এই দুই মতই সমান অগ্রাহ্য করেন; কেননা, এই দুয়ের মধ্যস্থ দল হচ্ছে কনগ্রেস। এ মতে শুদ্ধ-স্বরাজ্য সম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ হতে পারে, কিন্তু সাম্রাজ্যের ভিতর স্বরাজ্য’-সম্বন্ধে হতে পারে না। কেননা, সাম্রাজ্যের ভিতর স্বরাজ্য যে খাপ খাওয়ানো যেতে পারে, তার উদাহরণ ক্যানাডা অস্ট্রেলিয়া সাউথ-আফ্রিকা প্রভৃতি। সুতরাং যার এত নজির আছে, সেই আদর্শের পক্ষে ওকালতি করায় বাধা নেই; অতএব এ আদর্শ বিদ্যাসংগতও বটে, বুদ্ধিসংগতও বটে; কেননা, যদি বর্তমানের উপাদান নিয়ে ভবিষ্যতের মতি গড়তে হয়, তাহলে এছাড়া অন্যকোনো আদর্শ হতে পারে না। তবে এই আদর্শকে বিপক্ষ-পক্ষ হেসে এই প্রশ্ন করেন যে—
‘তুমি কোন গগনের ফল,
তুমি কোন বামনের চাঁদ’
এর উত্তরে স্বয়ং প্রশ্নকর্তাই বলেন যে, আদর্শ ইংরেজি-শিক্ষিত ভারতবর্ষের চিদ-আকাশের ফল এবং ইংরেজি-শিক্ষিত ভারতবর্ষের অমাবস্যার চাঁদ।
একথা শুনে কনগ্রেস বলেন, এ ভবিষ্যতের আদর্শ এবং সে ভবিষ্যৎও এত দর-ভবিষ্যৎ যে, বর্তমানের ধলো যাঁদের চোখে ঢুকেছে, সেইসকল অধলোকেই এর সাক্ষাৎ পান না বলে এর অস্তিত্বেও বিশ্বাস করেন না। এ আদর্শ ভারতবর্ষের কল্পনার ধন। এ তো হাতে নাগাল পাবার জিনিস নয়, মনশ্চক্ষে দরবীন ক’ষে এ আদর্শ দেখতে হয়। কনগ্রেসের সকল বাণীই যে ভবিষ্যদ্বাণী, এ জ্ঞান থাকলে বিপক্ষ-পক্ষ কনগ্রেসের কথা শুনে আর হাসত না।
ভবিষ্যতে কি হতে পারে আর না হতে পারে, সেবিষয়ে ত্রিকালজ্ঞ স্বয়ং ভগবান ছাড়া আর কেউ কিছু বলতে পারেন না। সুতরাং দর-ভবিষ্যতে যে ঐ আদর্শ-চাঁদ ভারতবাসীর হাতে আসবে না এবং তাদের মাথায় ঐ আকাশকুসুমের পপটি হবে না–একথা জোর করে কে বলতে পারে। তবে এখন ঐ চাঁদকে ডেকে ‘আয় আয় আমাদের মাথায় টী দিয়ে যা, আর ঐ আকাশকুমকে ডেকে যেখানে আছ সেখানেই থাকো, দেখো যেন ঝরে আমাদের গায়ে পড়ো না’–একথা বলা ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর নেই। কেননা, বেশি আলোয় আমাদের চোখ ঝলসে যায়, আর আমরা ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাই।
তবে কথা হচ্ছে এই যে, বর্তমানকে আমরা একেবারেই উপেক্ষা করতে পারি নে, কেননা এ পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যা সম্বন্ধ তা বর্তমানেরই সম্বন্ধ। ‘চোখ বুজলেই অন্ধকার’–এ প্রবাদ তো সকলেই জানেন। সুতরাং আমাদের খোলা-চোখের জন্যও একটা আদর্শ থাকা দরকার। আমরা চাই সেই ফল, যার দ্বারা মা’র নিত্যপজা চলবে; আর সেই চাঁদ, যার আলোতে আমরা রাত্তিরে পথ দেখতে পাব। বলা বাহুল্য যে, এদেশে এখন রাত্তির, আর আমরা জাতকে-জাত রাত-কানা।।
অতএব কগ্রেসের পক্ষে জাতীয়-রাজনৈতিক-শিক্ষা-পরিষদ, হবার পূর্বে জাতীয়-রাজনৈতিক-আদর্শ-অনুসন্ধান-সমিতি হওয়া কর্তব্য।
ইতিমধ্যে আমি একটি আটপৌরে আদর্শ দেশের হাতে ধরে দিতে চাই। আমার কথা এই–এস, আমরা ঘরে বসে নিজের নিজের চরকায় বিলেতি তেল দিই, তাহলেই সকলে মিলে ভারতমাতার চরকায় স্বদেশী তেল দেওয়া হবে এবং তাতে মা আমাদের যে কাটনা কাটবেন, তার সততা মাকড়সার সুতোর চাইতে সূক্ষ্ণ হবে এবং সেই সুতোর জাল বুনে সেই ফাঁদে আমরা আকাশের চাঁদ ধরব।
ফাগুন ১৩২২
কৈফিয়ত
সম্প্রতি বঙ্গসাহিত্যের ছোট বড় মাঝারি সকলরকম সমালোচক আমার ভাষার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করছেন। সে প্রতিবাদে নানাজাতীয় নানা পত্র মুখরিত হয়ে উঠেছে। সে মরমর-ধনি শুনে আমি ভীত হলেও চমকিত হই নি; কেননা, আমি যখন বাংলা লেখায় দেশের পথ ধরে চলছি তখন অবশ্য সাহিত্যের রাজপথ ত্যাগ করেছি। যথভ্রষ্ট লেখককে সাহিত্যের দলপতিরা যে ভ্রষ্ট বলবেন, এতে আর আশ্চর্য কি। বিশেষত সে রাজপথ যখন শুধু পাকা নয়–সংস্কৃতভাঙা শরকি বিলেতি-মাটি এবং চুন দিয়ে একেবারে শানবাঁধানো রাস্তা। অনেকের বিশ্বাস যে, সাহিত্যের এই সদর-রাস্তাই হচ্ছে একমাত্র সাধু পথ, বাদবাকি সব গ্রাম্য। তবে জিজ্ঞাস্যবিষয় এইটকু যে, এই গ্রাম্যতার অপবাদ আমার ভাষার প্রতি সম্প্রতি দেওয়া হচ্ছে কেন। আমি প্রবীণ লেখক না হলেও নবীন লেখক নই। আমি বহনকাল ধরে বাংলা কালিতেই লিখে আসছি। সে কালির ছাপ আমার লেখার গায়ে চিরদিনই রয়েছে। আমার রচনার যে ভঙ্গিটি সহদয় পাঠক এবং সমজদার সমালোচকেরা এতদিন হয় নেকনজরে দেখে এসেছেন, নয় তার উপর চোখ দেন নি—আজ কেন সকলে তার উপর চোখ-লাল করছেন। এর কারণ আমি প্রথমে বুঝে উঠতে পারি নি।
এখন শুনছি, সে, ভাষার নবাবিষ্কৃত দোষ এই যে তা ‘সবুজপত্রের ভাষা’। সবুজের, তা দোষই বল আর গণই বল, একটি বিশেষ ধর্ম আছে। ইংরেজেরা বলেন, যে চোখে সে রঙের আলো পড়ে, সে চোখের কাছে অপরের কোনো দোষই ছাপা থাকে না। আমাদের দোষ যাই হোক, তা যে গুণীসমাজে মারাত্মক বলে বিবেচিত হয়েছে, তার প্রমাণ এই যে, পরিষত্মন্দিরে স্বয়ং বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় ‘সবুজপত্রের ভাষার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করতে বাধ্য হয়েছিলেন’। এ সংবাদ শুনে উক্ত পত্রের সম্পাদকের নিশ্চয়ই হরিষে-বিষাদ উপস্থিত হয়েছে। পালমহাশয়ের ন্যায় খ্যাতনামা ব্যক্তি যার লেখা আলোচনার যোগ্য মনে করেন, তার কলম-ধরা সার্থক; কেননা, এতেই প্রমাণ হয় যে, তার লেখায় প্রাণ আছে। যা মত, একমাত্র তাই নিন্দা-প্রশংসার বহির্ভূত। অপরপক্ষে বিষন্ন হবার কারণ এই যে, যেষাং পক্ষে জনাদন’ সেই পাণ্ডুপুত্রদের জয় এবং সবুজপত্রের পরাজয়ও অবশ্যম্ভাবী।
পালমহাশয় যে সবপত্রের ভাষার উপর আক্রমণ করেছেন, এ রিপোর্ট নিশ্চয়ই ভুল : কেননা, ও-পত্রের কোনো বিশেষ ভাষা নেই। উক্ত পত্রের ভিন্ন ভিন্ন লেখকদের রচনার পদ্ধতি ও রীতি সবই পথক। পদের নির্বাচন ও তার বিন্যাস প্রতি লেখক নিজের রুচি অনুসারেই করে থাকেন। কাল যখন কলি, তখন লেখবার কলও নিশ্চয় রচিত হবে; কিন্তু ইতিমধ্যে সবুজপত্রের সম্পাদক যে সে-কলের সন্ধানলাভ করেছেন, এমন তো মনে হয় না। সকলের মনোভাব আর-কিছু একই ভাষার ছাঁচে ঢালাই করা যেতে পারে না। মানুষের জীবনের ও মনের ছাঁচ তৈয়ারি করা যাঁদের ব্যাবসা, তাঁরা অবশ্য একথা স্বীকার করবেন না; তাহলেও কথাটি সত্য। সংগচ্ছদ্ধং এই বৈদিক বিধির কর্মজীবনে যথেষ্ট সার্থকতা আছে। কিন্তু ‘সংবদধ্বং’ এই বিধির সাহিত্যে বিশেষ-কোনো সার্থকতা নেই। এই কারণেই সাহিত্যের প্রতি-লেখককেই তাঁর নিজের মনোভাব নিজের মনোমত ভাষায় প্রকাশ করবার স্বাধীনতা দেওয়া আবশ্যক। ‘সবুজপত্রে লেখকদের সে স্বাধীনতা যে আছে, তা উদাহরণের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, সবুজপত্রের নয়, আমার ভাষার উপরেই পালমহাশয় আক্রমণ করেছেন। আমার ভাষার রোগ মারাত্মক হতে পারে, কিন্তু তা সংক্রামক নয়। এক সবুজপত্রের সম্পাদক ব্যতীত আর-কেউই আমার পথানসেরণ কিংবা পদানকরণ করেন না। পালমহাশয় বঙ্গসাহিত্যের সর্বোচ্চ আদালতে আমার ভাষার বিরদ্ধে যে নালিশ রজ করেছেন, সম্ভবত তার একতরফা ডিক্রি হয়ে গেছে; কেননা, সে সময়ে আমি সেক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলাম না। উপস্থিত থাকলে যে মামলা ডিসমিস, করিয়ে নিতে পারতুম, তা নয়। পালমহাশয় বাক্যজগতে মহাবলী এবং মহাবলিয়ে। আমার এতাদশ বাকপটতা নেই যে, আমি তাঁর সঙ্গে বাগযুদ্ধে প্রবত্ত হতে সাহসী হই। আরজি যদি লিখিত হয়, তাহলে হয় তার লিখিত জবাবু নয় কবল-জবাবু দেওয়া যায়। কিন্তু বক্তৃতা হল ধম জ্যোতি সলিল ও মরতের সন্নিপাত। উড়ো-কথার সঙ্গে কোন্দল করতে হলে হাওয়ায় ফাঁদ পাতা আবশ্যক; সে বিদ্যে আমার নেই। তবে পালমহাশয় যখন এদেশের এ যুগের একজন অগ্রগণ্য গুণী, তখন তিনি আমাদের ন্যায় নগণ্য লেখকের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ উপস্থিত করলে আমরা তার কৈফিয়ত দিতে বাধ্য।
সংবাদপত্রের সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট থেকে ঠিক বোঝা গেল না যে, আমার ভাষার বিরুদ্ধে পালমহাশয়ের অভিযোগটি কি। আমি পবেই স্বীকার করেছি যে, আমার ভাষা আর-পাঁচজনের ভাষা হতে ঈষৎ পথক। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র দোষ বলে গণ্য হতে পারে না। কিং স্বাতন্ত্রম, অবলম্বসে’–এ ধমক সাহিত্যসমাজে কোনো গরজন কোনো ক্ষদ্রজনকে দিতে যে অধিকারী নন, পালমহাশয়ের ন্যায় বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির নিকট তা কখনোই অবিদিত নেই। তারপর কেউ-কেউ বলেন যে, আমি খাঁটি বাংলার পক্ষপাতী। কোনোরূপ খাঁটি জিনিসের পক্ষপাতী হওয়াই যে দোষ, একথাও বোধ হয় কেউ মুখ ফটে বলবেন না; বিশেষত যখন সে পদার্থ হচ্ছে মাতৃভাষা। মাতৃভাষার শক্তির উপর বিশ্বাস থাকাটাও যে একটা মহাপাতক— একথা আর যেই বলন না কেন, পালমহাশয় কখনো বলতে পারেন না। তবে খাঁটিমাল বলে যদি ভেজাল চালাবার চেষ্টা করি, তাহলে অবশ্য তার জন্য আমার জবাবদিহি আছে। যার সঙ্গে যা মেশানো উচিত নয়, গোপনে তার সঙ্গে তাই মেশালে ভেজাল হয়। ভেজালের মহা দোষ এই যে, তা উদরস্থ করলে মন্দাগ্নি হয়। কিন্তু আমার ভাষা যে, কারও-কারও পক্ষে অগ্নিবর্ধক, তার প্রমাণ এই যে, তা গলাধঃকরণ করামাত্র তাঁরা অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন। সে যাই হোক, মণিকাঞ্চনের যোগ সাহিত্যে নিন্দনীয় নয়। সোনার বাংলায় সংস্কৃতের হীরামানিক আমি যদি বসাতে না পেরে থাকি, তাহলে সে আমার অক্ষমতার দরুন; আমি কারিগর নই বলে যে সাহিত্যে জড়াও-কাজ চলবে না, তা হতেই পারে না। খাঁটি সংস্কৃত যে খাঁটি বাংলার সঙ্গে খাপ খায়, সেবিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। বাংলার গায়ে আলগা হয়ে বসে শুধু ইংরেজিভাঙা হাল সংস্কৃত, ওরফে সাধশব্দ। আমার ভাষা নাকি কলকাত্তাই ভাষা। সুতরাং উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম থেকে তা আক্রমণ করা সহজ। অপরপক্ষে সাধুভাষার জন্মস্থান হচ্ছে ফোর্ট উইলিঅমে, সতরাং তাকে আর আক্রমণ করা চলে না–সে যে কেল্লার ভিতরে বসে আছে।
শুনতে পাই যে, পালমহাশয়ের মতে আমার ভাষার প্রধান দোষ এই যে, তা দুর্বোধ। লিখিত ভাষা যে পরিমাণে মৌখিক ভাষার অনুরূপ হয়, সেই পরিমাণে যে তা দুর্বোধ হয়ে ওঠে–এ সত্য আমার জানা ছিল না। শ্ৰীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বলেন যে, সাধুভাষা লেখা সহজ। একথা সম্পূর্ণ সত্য। তবে যে আমি সাধুভাষার এই সহজ পথ ত্যাগ করে ‘ভাষামাগে ক্লেশ’ করি, তার কারণ আমার ধারণা যে, বাঙালি পাঠকের কাছে চলিত ভাষা সহজবোধ্য। যে প্রসাদগণের আরাধনা করার দরুন আমি সমালোচকদের প্রসাদে বঞ্চিত হয়েছি, সেই গুণের অভাবই যে ‘অসাধুভাষার প্রথম এবং প্রধান দোষ, একথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নি। অতএব আমার ভাষার যে এ দোষ আছে তা আমি বিনা আপত্তিতে মেনে নিতে পারি নি। তবে যদি পাঠক পড়বার সময় সে ভাষা মনে-মনে ইংরেজিতে তরজমা করে নিতে পারেন না বলে তার অর্থ গ্রহণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়, তাহলে অবশ্য আমার রচনা দুর্বোধ্য।
লোকে বলে পাঁজি যখন হাতে আছে আছে তখন বারটি মঙ্গল কি শনি সেবিষয়ে তর্ক করার অর্থ শুধু সময় এবং বুদ্ধিবৃত্তির অপব্যয় করা। আমি তাই আমার এবং পালমহাশয়ের লেখার নমুনা পাশাপাশি ধরে দিচ্ছি, পাঠকেরা বিচার করবেন যে, কোন অংশে আমার ভাষা বাদীর ভাষা অপেক্ষা অধিক দুর্বোধ। আমাদের উভয়েরই বক্তব্যবিষয়ের মিল আছে, সুতরাং ভাষার তারতম্য সহজেই চোখে পড়বে।–
‘যৌবনে দাও রাজটিকা’
বীরবল
এদেশে জ্ঞানীব্যক্তিদিগের মতে মনের বসন্তঋতু ও প্রকৃতির যৌবনকাল, দুই অশায়েস্তা, অতএব শাসনযোগ্য।…সেই কারণে জ্ঞানীব্যক্তিরা আমাদের প্রকৃতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বারণ করেন, এবং নিত্যই আমাদের প্রকৃতির উলটো টান টানতে পরামর্শ দেন; এই কারণেই মানুষের যৌবনকে বসন্তের প্রভাব হতে দূরে রাখা আবশ্যক।… আমাদের বিশ্বাস মানবজীবনে যৌবন একটা মস্ত ফাঁড়া–কোনোরকমে সেটি কাটিয়ে উঠতে পারলেই বাঁচা যায়। এ অবস্থায় কি জ্ঞানী কি অজ্ঞানী সকলেই চান যে, একলম্ফে বাল্য হতে বার্ধক্যে উত্তীর্ণ হন।
২.
মনুষ্যত্ব খর্ব করে মানবসমাজটাকে টবে জিইয়ে রাখায় যে বিশেষ-কিছু, অহংকার করবার আছে, তা আমার মনে হয় না।
৩.
দেহের যৌবনের অন্তে বার্ধক্যের রাজ্যে যৌবনের অধিকার বিস্তার করবার শক্তি আমরা সমাজ হতেই সংগ্রহ করতে পারি।… সমগ্র সমাজের এই জীবনপ্রবাহ যিনি নিজের অন্তরে টেনে নিতে পারবেন, তাঁর মনের যৌবনের আর ক্ষয়ের আশঙ্কা নেই।
–সবুজপত্র, জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
যৌবনে কৃষ্ণকথা
শ্ৰীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল
অক্ষয়বাবু বলিয়াছেন ‘যৌবন বিষম কাল’ কিন্তু চারপাঠ পড়িয়াও আমরা যৌবনের বিষমত্বটা অনুভব করি নাই। আজিকালিকার নবযুবকদিগকে দেখিয়া মনে হয় যেন এদেশ হইতে বসন্তের মতন যৌবনও একরপ চিরবিদায় লইয়াছে।… চক্ষে দেখি তিনটা ঋতু গ্রীষ্ম বর্ষা আর শীত। কিন্তু বসন্তের সাক্ষাৎকার পাওয়া একরূপ অসাধ্য। সেইরূপ এদেশে মানুষের জীবনেও বাল্য প্রৌঢ় ও বার্ধক্য, এই তিন কালই দেখা যায়। বাল্য ফুরাইতে না ফুরাইতে । প্রৌঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।
২.
টবেতে বড় গাছ জন্মায় না ও বাড়ে না, সেরূপ এক একটা ধর্মের ও নীতির টব সাজাইয়া মানুষগুলোকে তাতে পুঁতিয়া রাখিলে তাদের মনুষ্যত্বও ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায় না।
৩.
যেসকল যুবক এই যৌবনের সংকেত পাইয়াছিলেন, তাঁরা আজি পর্যন্ত তেমন বুড়া হইতে পারেন নাই। বিদ্যাসাগর প্রভৃতির যৌবন আমরণ পর্যন্ত বাঁচিয়াছিল। কর্মবীর অশ্বিনীকুমার ও সুরসিক মনোরঞ্জন, ইহাদের দেখিয়া বয়সের সঙ্গে যৌবনের কোনও অপরিহার্য সম্বন্ধ আছে, এমন মনে হয় না। এঁরা এখনও যৌবনের জের টানিতেছেন।
–প্রবাহিনী, ৯ শ্রাবণ ১৩২১
এর কোন পাশে আলো আর কোন পাশে ছায়া, তার বিচার পাঠকসমাজই করবেন।
ধ্বনির অপেক্ষা প্রতিধ্বনি যদি বেশি স্পষ্ট হয়, তাহলে অবশ্য পালমহাশয়ের ভাষা আমার ভাষা অপেক্ষা বেশি স্পষ্ট।
আসল কথা, ভাষার বিচার শুধু বাগবিতণ্ডায় পরিণত হয়, যদি-না আমরা ধরতে পারি যে, তথাকথিত সাধুভাষার সঙ্গে তথাকথিত অসাধুভাষার পার্থক্যটি কোথায় এবং কতদূর।
শ্ৰীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বলেছেন যে, আর-পাঁচজনে যে ভাষায় লেখেন, আমিও সেই একই ভাষায় লিখি; তফাৎ এইটুকু যে, ক্রিয়াপদ এবং সর্বনামের ব্যবহার আমি মৌখিক ভাষার অনুরুপই করে থাকি। চলমহাশয়ের মত আমি শিরোধার্য করি; কেননা, তাঁর একথা সম্পূর্ণ সত্য।
আমি ‘তাহার’ পরিবর্তে ‘তার’ লিখি, অর্থাৎ সাধু সর্বনামের হৃদয়ের হা বাদ দিই। ‘হায় হায়’ বাদ দিলে বাংলায় যে পদ্য হয় না, তা জানি; কিন্তু ‘হা হা’ বাদ দিলে যে গদ্য হয় না, এ ধারণা আমার ছিল না। এবিষয়ে কিন্তু পালমহাশয় আমার সঙ্গে একমত; কেননা, তাঁর লেখাতেও উক্ত ‘হা’ উহ্য থেকে যায়।
শেষটা দাঁড়াল এই যে, পালমহাশয়ের ভাষার সঙ্গে আমার ভাষার যা-কিছু প্রভেদ, তা হচ্ছে ক্রিয়ার বিভক্তিগত। আমি লিখি ‘করে’, তিনি লেখেন ‘করিয়া’। ‘করে’র বদলে ‘করিয়া’ লিখলেই যে ভাষা সমাজিত হয়ে ওঠে, এ বিশ্বাস আমার থাকলে আমি সাহিত্যের সাধুপথ কখনোই ত্যাগ করতুম না। আমার বিশ্বাস, অত শস্তা উপায়ে সুলেখক হওয়া যায় না, কেননা এক স্বরবর্ণের গুণে শব্দের ব্যঞ্জনাশক্তি তাদশ বন্ধিলাভ করে না।
শ্ৰীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার তাঁর অভিভাষণে বলেছেন যে, ‘এ এ’ আর ‘ইয়ে ইয়ে’ এ দুয়ের ভিতর ভাষার কোনো প্রভেদ নেই, প্রভেদ যা আছে তা বানানের। একথা যদি সত্য হয়, এবং আমার বিশ্বাস তা সত্য, তাহলে পালমহাশয়ের আমার ভাষার উপর যে আক্রমণ, তা আসলে বানানের উপরে গিয়েই পড়েছে। বানান আমার কাছে চিরদিনই একটি মহা সমস্যা, এবং সে সমস্যার উত্তর-মীমাংসা করা আমার সাধ্যের অতীত। অসাধুভাষার বিপদ যেমন এই বানানের দিকে, সাধুভাষারও বিপদ তেমনি বানানোর দিকে। ও ভাষায় লিখতে বসলে যখন পালমহাশয়ের চাঁচা কলমের মুখ ফসকে ‘আমরণ পর্যন্ত বাঁচিয়াছিল’ এইরূপ বাক্য বেরিয়ে পড়ে, তখন আমাদের কাঁচা কলমের উপর ভরসা কি? এহেন সাধহস্ত হতে মুক্তিলাভ না করলে বঙ্গসরস্বতী ‘আমরণ পর্যন্ত বাঁচিয়া’ নয়, মরিয়াই থাকিবে।
আশ্বিন ১৩২১
খেয়ালখাতা
শ্ৰীমতী ‘ভারতী’সম্পাদিকা নূতন বৎসরের প্রথম দিন হতে ভারতীর জন্য একটি খেয়ালখাতা খুলবেন। এই অভিপ্রায়ে যাঁরা লেখেন কিংবা লিখতে পারেন, কিংবা যাঁদের লেখা উচিত কিংবা লিখতে পারা উচিত— এমন অনেক লোকের কাছে দু-এক কলম লেখার নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন। উপরোক্ত চারটি দলের মধ্যে আমি যে ঠিক কোথায় আছি, তা জানি নে। তবও ভারতীসম্পাদিকার সাদর নিমন্ত্রণ রক্ষা করা কর্তব্য বিবেচনায় দুচার ছত্র রচনা করতে উদ্যত হয়েছি। ভারতীসম্পাদিকা ভরসা দিয়েছেন যে, যা-খুশি লিখলেই হবে; কোনো বিশেষ বিষয়ের অবতারণা কিংবা আলোচনা করবার দরকার নেই। এ প্রস্তাবে অপরের কি হয় বলতে পারি নে, আমার তো ভরসার চাইতে ভয় বেশি হয়। আমাদের মন সহজে এবং শিক্ষার গুণে এতটা বৈষয়িক যে, বিষয়ের অবলম্বন ছেড়ে দিলে আমাদের মনের ক্রিয়া বন্ধ হয়, বলবার কথা আর কিছু থাকে না। হাওয়ার উপর চলা যত সহজ, ফাঁকার উপর লেখাও তত সহজ। গণিতশাস্ত্রে যাই হোক, সাহিত্যে শূন্যের উপর শূন্য চাপিয়ে কোনো কথার গুণবৃদ্ধি করা যায় না। বিনিসুতার মালার ফরমাস দেওয়া যত সহজ, গাঁথা তত সহজ নয়। ও বিদ্যের সন্ধান শতেকে অনেক জানে। আসল কথা, আমরা সকলেই গভীর নিদ্রামগ্ন, শুধু কেউ কেউ স্বপ্ন দেখি। ভারতীসম্পাদিকার ইচ্ছা, এই শেষোক্ত দলের একটু বকবার সুবিধে করে দেওয়া।
২.
এ খেয়ালখাতা ভারতীর চাঁদার খাতা। স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দচিত্তে যিনি যা দেবেন, তা সাদরে গ্রহণ করা হবে। আধুলি শিকি দুআনি কিছুই ফেরৎ যাবে না, শুধু ঘষা পয়সা ও মেকি চলবে না। কথা যতই ছোট হোক, খাঁটি হওয়া চাই তার উপর চকচকে হলে তো কথাই নেই। যে ভাব হাজার হাতে ফিরেছে, যার চেহারা বলে জিনিসটে লুপ্তপ্রায় হয়েছে, অতি পরিচিত বলে যা আর-কারও নজরে পড়ে না, সে ভাব এ খেয়ালখাতায় স্থান পাবে না। নিতান্ত পরননা চিন্তা, পুরনো ভাবের প্রকাশের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে–আর্টিকেল লেখা। আমাদের কাজের কথায় যখন কোনো ফল ধরে না, তখন বাজে-কথার ফুলের চাষ করলে হানি কি। যখন আমাদের ক্ষুধানিবৃত্তি করবার কোনো উপায় করতে পারছি নে, তখন দিন থাকতে শখ মিটিয়ে নেবার চেষ্টা করাটা আবশ্যক। আর একথা বলা বাহুল্য, যেখানে কেনাবেচার কোনো সম্বন্ধ নেই ব্যাপারটা হচ্ছে শুধু দান ও গ্রহণের সেস্থলে কোনো ভদ্রসন্তান মসিজীবী হলেও, যেকথা নিজে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন না কিংবা ঝুটো বলে জানেন, তা চালাতে চেষ্টা করবেন না। আমরা কার্যজগতে যখন সাচ্চা হতে পারি নে, তখন আশা করা যায় কল্পনাজগতে অলীকতার চর্চা করব না। এই কারণেই বলছি, ঘষা পয়সা ও মেকি চলবে না।
৩.
খেয়ালী লেখা বড় দুষ্প্রাপ্য জিনিস। কারণ সংসারে বদখেয়ালী লোকের কিছু কমতি নেই, কিন্তু খেয়ালী লোকের বড়ই অভাব। অধিকাংশ মানুষ যা করে তা আয়াসসাধ্য; সাধারণ লোকের পক্ষে একটুখানি ভাব, অনেকখানি ভাবনার ফল। মানুষের পক্ষে চেষ্টা করাটাই স্বাভাবিক, সুতরাং সহজ। স্বতঃউচ্ছসিত চিন্তা কিংবা ভাব শুধু দু-এক জনের নিজ প্রকৃতিগণে হয়। যা আপনি হয় তা এতই শ্রেষ্ঠ ও এতই আশ্চর্যজনক যে, তার মূলে আমরা দৈবশক্তি আরোপ করি। এ জগৎসৃষ্টি ভগবানের লীলা বলেই এত প্রশস্ত, এবং আমাদের হাতে-গড়া জিনিস কষ্টসাধ্য বলেই এত সংকীর্ণ। তবে আমাদের সকলেরই মনে বিনা ইচ্ছাতেও যে নানাপ্রকার ভাবনাচিন্তার উদয় হয়, একথা অস্বীকার করবার জো নেই। কিন্তু সে ভাবনাচিন্তার কারণ স্পষ্ট এবং রূপ অস্পষ্ট। রোগ শোক দারিদ্র্য প্রভৃতি নানা স্পষ্ট সাংসারিক কারণে আমাদের ভাবনা হয়; কিন্তু সে ভাবনা এতই এলোমেলো যে, অন্যে পরে কা কথা, আমরা নিজেরাই তার খেই খুঁজে পাই নে। যা নিজে ধরতে পারি নে, তা অন্যের কাছে ধরে দেওয়া অসম্ভব; যে ভাব আমরা প্রকাশ করতে পারি নে, তাকে খেয়াল বলা যায় না। খেয়াল অনির্দিষ্ট কারণে মনের মধ্যে দিব্য একটি সস্পষ্ট সসম্বদ্ধ চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়। খেয়াল রূপবিশিষ্ট, দুশ্চিন্তা তা নয়।
৪.
খেয়াল অভ্যাস করবার পূর্বে খেয়ালের রূপনির্ণয় করাটা আবশ্যক, কারণ স্বরূপ জানলে অনধিকারীরা এবিষয়ের বৃথা চর্চা করবেন না। আমাদের লিখিত-শায়ে খেয়ালের বড় উদাহরণ পাওয়া যায় না, সুতরাং সংগীতশাস্ত্র হতে এর আদর্শ নিতে হবে। এককথায় বলতে গেলে, ধ্রুপদের অধীনতা হতে মুক্ত হবার বাসনাই খেয়ালের উৎপত্তির কারণ। ধ্রুপদের ধীর গম্ভীর শুদ্ধ শান্ত রূপ ছাড়াও পৃথিবীতে ভাবের অন্য অনেক রূপ আছে। বিলম্বিত লয়ের সাহায্যে মনের সকল স্ফূর্তি, সকল আক্ষেপ প্রকাশ করা যায় না। সুতরাং ধ্রুপদের কড়া শাসনের মধ্যে যার স্থান নেই, যথা তান গিটকিরি ইত্যাদি, তাই নিয়েই খেয়ালের আসল কারবার। কিন্তু খেয়ালের স্বাধীন ভাব উচ্ছল হলেও যথেচ্ছাচারী নয়। খেয়ালী যতই কাদানি করুন না কেন, তালচ্যুত কিংবা রাগভ্রষ্ট হবার অধিকার তাঁর নেই। জড় যেমন চৈতন্যের আধার, দেহ যেমন রূপের আশ্রয়ভূমি, রাগও তেমনি খেয়ালের অবলম্বন। বর্ণ ও অলংকার-বিন্যাসের উদ্দেশ্য রূপ ফুটিয়ে তোলা, লুকিয়ে ফেলা নয়। খেয়ালের চাল ধ্রুপদের মত সরল নয় বলে মাতালের মত আঁকাবাঁকা নয়, নতকীর মত বিচিত্র। খেয়াল ধ্রুপদের বন্ধন যতই ছাড়িয়ে যাক না কেন, সরের বন্ধন ছাড়ায় না; তার গতি সময়ে সময়ে অতিশয় দ্রুতলঘ, হলেও ছন্দঃপতন হয় না। গানও যে নিয়মাধীন, লেখাও সেই নিয়মাধীন। যাঁর মন সিধে পথ ভিন্ন চলতে জানে না, যাঁর কল্পনা আপনা হতেই খেলে না, যিনি আপনাকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে পারেন না, অথবা ছেড়ে দিলে আর নিজবশে রাখতে পারেন না তাঁর খেয়াল লেখার চেষ্টা না করাই ভালো। তাতে তাঁর শুধু গৌরবের লাঘব হবে। কৃশদেহ পুষ্ট করবার চেষ্টা অনেক সময়ে ব্যর্থ হলেও কখনোই ক্ষতিকর নয়, কিন্তু খুলদেহকে সক্ষম করবার চেষ্টায় প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়। ইঙ্গিতজ্ঞ লোকমাত্রেই উপরোক্ত কথাকটির সার্থকতা বুঝতে পারবেন।
৫.
আমার কথার ভাবেই বুঝতে পারছেন যে, আমি খেয়াল-বিষয়ে একটু হালকা অঙ্গের জিনিসের পক্ষপাতী। চুটকিও আমার অতি আদরের সামগ্রী, যদি সুর খাঁটি থাকে ও ঢং ওস্তাদী হয়। আমার বিশ্বাস আমাদের দেশের আজকাল প্রধান অভাব গুণপনাযুক্ত ছিবলেমি। এ সম্বন্ধে কৈফিয়তস্বরূপে দু-এক কথা বলা প্রয়োজন। কোনো ব্যক্তি কিংবা জাতি বিশেষ যখন অবস্থা: বিপর্যয়ে সকল অধিকার হতে বিচ্যুত হয়, তখন তার দুটি অধিকার অবশিষ্ট থাকে— কাঁদবার ও হাসবার। আমরা আমাদের সেই কাঁদবার অধিকার ষোলোআনা বুঝে নিয়েছি এবং নিত্য কাজে লাগাচ্ছি। আমরা কাঁদতে পেলে যত খুশি থাকি, এমন আর কিছুতেই নয়। আমরা লেখায় কাঁদি, বক্তৃতায় কাঁদি। আমরা দেশে কেঁদেই সন্তুষ্ট থাকি নে, চাঁদা তুলে বিদেশে গিয়ে কাঁদি। আমাদের স্বজাতির মধ্যে যাঁরা স্থানে-অস্থানে, এমনকি অরণ্যে পর্যন্ত, রোদন করতে শিক্ষা দেন, তাঁরাই দেশের জ্ঞানী গুণী বুদ্ধিমান ও প্রধান লোক বলে গণ্য এবং মান্য। যেখানে ফোঁস করা উচিত, সেখানে ফোঁসফোঁস করলেই আমরা বলিহারি যাই। আমাদের এই কান্না দেখে কারও মন ভেজে না, অনেকের মন চটে। আমাদের নূতন সভ্যযুগের অপর্ব সৃষ্টি ন্যাশনেল কনগ্রেস, অপর সদ্যজাত শিশুর মত ভূমিষ্ঠ হয়েই কান্না শুরু করে দিলেন। আর যদিও তার সাবালক হবার বয়স উত্তীর্ণ হয়েছে, তবুও বৎসরের তিন শ বাষট্টি দিন কুম্ভকর্ণের মত নিদ্রা দিয়ে, তারপর জেগে উঠেই তিন দিন ধরে কোকিয়ে কান্না সমান চলছে। যদি কেউ বলে, ছি, অত কাঁদ কেন, একটু কাজ কর না। তাহলে তার উপর আবার চোখ রাঙিয়ে ওঠে। বয়সের গুণে শুধু ঐটুকু উন্নতি হয়েছে। মনের দুঃখের কান্নাও অতিরিক্ত হলে কারও মায়া হয় না। কিন্তু কান্নাব্যাপারটাকে একটা কত ব্যকর্ম করে তোলা শুধু আমাদের দেশেই সম্ভব হয়েছে। আমরা সমস্ত দিন গহকর্ম করে বিকেলে গা-ধুয়ে চুল-বেধে পা-ছড়িয়ে যখন পুরাতন মাতৃবিয়োগের জন্য নিয়মিত এক ঘণ্টা ধরে ইনিয়েবিনিয়ে কাঁদতে থাকি, তখন পৃথিবীর পুরুষমানুষদের হাসিও পায়, রাগও ধরে। সকলেই জানেন যে, কান্নাব্যাপারটারও নানা পদ্ধতি আছে, যথা রোলকান্না, মড়াকান্না, ফুপিয়ে কান্না, ফলেফুলে কান্না ইত্যাদি। কিন্তু আমরা শুধু অভ্যাস করেছি নাকে-কান্না। এবং একথাও বোধ হয় সকলেই জানেন যে, সদারঙ্গ বলে গেছেন–খেয়ালে সব সুর লাগে, শুধু নাকী সুর লাগে না। এইসব কারণেই আমার মতে এখন সাহিত্যের সুর বদলানো প্রয়োজন। করণরসে ভারতবর্ষ স্যাঁতসেতে হয়ে উঠেছে; আমাদের সুখের জন্য না হোক, স্বাস্থ্যের জন্যও হাস্যরসের আলোক দেশময় ছড়িয়ে দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে। যদি কেউ বলে, আমাদের এই দুর্দিনে হাসি কি শোভা পায়। তার উত্তর, ঘোর মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রিতেও কি বিদ্যৎ দেখা দেয় না, কিংবা শোভা পায় না। আমাদের এই অবিরতধারা অবষ্টির মধ্যে কেহ-কেহ যদি বিদ্যৎ সৃষ্টি করতে পারেন, তাহলে আমাদের ভাগ্যাকাশ পরিষ্কার হবার একটা সম্ভাবনা হয়।
বৈশাখ ১৩১২
চুটকি
সমালোচকেরা আমার রচনার এই একটি দোষ ধরেন যে, আমি কথায়কথায় বলি হচ্ছে। এটি যে একটি মহাদোষ সেবিষয়ে আর সন্দেহ নেই; কেননা, ওকথা বলায় সত্যের অপলাপ করা হয়। সত্যকথা বলতে গেলে বলতে হয়, বাংলায় কিছু হচ্ছে না। এদেশের কর্মজগতে যে কিছু হচ্ছে না, সে তো প্রত্যক্ষ; কিন্তু মনোজগতেও যে কিছু হচ্ছে না, তার প্রমাণ বর্ধমানের গত সাহিত্যসম্মিলন।
উক্ত মহাসভার পঞ্চ সভাপতি সমস্বরে বলেছেন যে, বাংলায় কিছু হচ্ছে না দর্শন, না বিজ্ঞান, না সাহিত্য, না ইতিহাস।
শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের প্রধান বক্তব্য এই যে, আমরা না-পাই সত্যের সাক্ষাৎ, না-করি সত্যাসত্যের বিচার। আমরা সত্যের স্রষ্টাও নই, দ্রষ্টাও নই; কাজেই আমাদের দর্শন-চর্চা realও নয়, criticalও নয়।
অধ্যাপক শ্ৰীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে, কি মত-বিজ্ঞান কি ‘অমত-বিজ্ঞান’, এ দুয়ের কোনোটিই বাঙালি অদ্যাবধি আত্মসাৎ করতে পারে নি; অর্থাৎ বিজ্ঞানের যন্ত্রভাগও আমাদের হাতে পড়ে নি, তার তন্ত্রভাগও আমাদের মনে ধরে নি। আমরা শুধু বিজ্ঞানের স্থূলসূত্রগুলি কণ্ঠ করেছি, এবং তার পরিভাষার নামতা মুখস্থ করেছি। যে বিদ্যা প্রয়োগপ্রধান, কেবলমাত্র তার মন্ত্রের শ্রবণে এবং উচ্চারণে বাঙালিজাতির মোক্ষলাভ হবে না। এককথায় আমাদের বিজ্ঞানচর্চা real নয়।
শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের মতে ইতিহাস-চর্চার উদ্দেশ্য সত্যের আবিষ্কার এবং উদ্ধার; এ সত্য নিত্য এবং গপ্ত সত্য নয়, অনিত্য এবং লুপ্ত সত্য। অতএব এ সত্যের দর্শন লাভের জন্য বিজ্ঞানের সাহায্য আবশ্যক। অতীতের জ্ঞানলাভ করবার জন্য হীরেন্দ্রবাবুর বর্ণিত বোধির (intuition) প্রয়োজন নেই প্রয়োজন আছে শুধু শিক্ষিত বুদ্ধির। অতীতের অন্ধকারের উপর বৃদ্ধির আলো ফেলাই হচ্ছে ঐতিহাসিকের একমাত্র কর্তব্য, সে অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া নয়। অথচ আমরা সে অন্ধকারে শুধু ঢিল নয়, পাথর ছড়ছি। ফলে পর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণের ঐতিহাসিকদের দেহ পরস্পরের শিলাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ছে। এককথায় আমাদের ইতিহাসচর্চা critical নয়।
অতএব দেখা গেল যে, সম্মিলনের সকল শাখাপতি এবিষয়ে একমত যে, কিছু হচ্ছে না। কিন্তু কি যে হচ্ছে, সেকথা বলেছেন স্বয়ং সভাপতি। তিনি বলেন, বাংলাসাহিত্যে যা হচ্ছে, তার নাম চুটকি। একথা লাখ কথার এক কথা। সকলেই জানেন যে, যখন আমরা ঠিক কথাটি ধরতে না পারি, তখনই আমরা লাখ কথা বলি। এই ‘চুটকি’-নামক বিশেষণটি খুঁজে না পাওয়ায় আমরা বগসরস্বতীর গায়ে ‘বিজাতীয় ‘অভিজাতীয়’ ‘অবাস্তব’ ‘অবান্তর’ প্রভৃতি নানা নামের ছাপ মেরেছি, অথচ তার প্রকৃত পরিচয় দিতে পারি নি।
তার কারণ, এসকল ছোট-ছোট বিশেষণের অর্থ কি, তার ব্যাখ্যা করতে বড়-বড় প্রবন্ধ লিখতে হয়; কিন্তু চুটকি যে কি পদার্থ, তা যে আমরা সকলেই জানি, তার প্রমাণ হাতে-হাতেই দেওয়া যায়।
শ্ৰীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের অভিভাষণ যে চুটকি নয়, একথা স্বয়ং শাস্ত্রীমহাশয়ও স্বীকার করতে বাধ্য; কেননা, একথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, ভাবে ও ভাষায় এর চাইতে ভারি অঙ্গের গদ্যবন্ধ জমানির বাইরে পাওয়া দুষ্কর।
হীরেন্দ্রবাবুর অভিভাষণও চুটকি নয়। তবে শাস্ত্রীমহাশয় এ মতে সায় দেবেন কি না জানিনে; কেননা, হীরেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ একে সংক্ষিপ্ত তার উপর আবার সহজবোধ্য, অর্থাৎ সকল দেশের সকল যুগের সকল দার্শনিক তত্ত্ব যেপরিমাণে বোঝা যায়, হীরেন্দ্রবাবুর দার্শনিক তত্ত্বও ঠিক সেই-পরিমাণে বোঝ যায় তার কমও নয় বেশিও নয়। শাস্ত্রীমহাশয়ের মতে যে-কাব্য মহাকায় তাই হচ্ছে মহাকাব্য। গজমাপে যদি সাহিত্যের মর্যাদা নির্ণয় করতে হয়, তাহলে হীরেন্দ্রবাবুর রচনা অবশ্য চুটকি; কেননা, তার ওজন যতই হোক না কেন, তার আকার ছোট।
অপরপক্ষে শাস্ত্রীমহাশয়ের অভিভাষণযুগল যে চুটকি-অঙ্গের, সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।
শাস্ত্রীমহাশয়ের নিজের কথা এই—’একখানি বই পড়িলাম, অমনি আমার মনের ভাব আমূল পরিবর্তন হইয়া গেল, যতদিন বাঁচিব ততদিন সেই বইয়ের কথাই মনে পড়িবে, এবং সেই আনন্দেই বিভোর হইয়া থাকিব’— এরকম যাতে হয় না, তারই নাম চুটকি। একথা যদি সত্য হয়, তাহলে জিজ্ঞাসা করি, বাংলায় এরকম ক’জন পাঠক আছেন যাঁরা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন যে, শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রবন্ধ পড়ে তাঁদের ভিতরটা সব ওলটপালট হয়ে গেছে।
শাস্ত্রীমহাশয় বাংলাসাহিত্যে চুটকির চেয়ে কিছু বড় জিনিস চান। বড় বইয়ের যদি ধর্মই এই হয় যে, তা পড়বামাত্র আমাদের মনের ভাবের আমল পরিবর্তন হয়ে যাবে, তাহলে সেরকম বই যত কম লেখা হয় ততই ভালো; কারণ দিনে একবার করে যদি পাঠকের অন্তরাত্মার আমূল পরিবর্তন ঘটে, তাহলে বড় বই লেখবার লোক যেমন বাড়বে, পড়বার লোকও তেমনি কমে আসবে। তিনি চুটকির সম্বন্ধে যে দুটি ভালো কথা বলেন নি তা নয়, কিন্তু সে অতি মুরবিয়ানা করে। ইংরেজেরা বলেন, স্বল্পস্তুতির অর্থ অতিনিন্দা। সুতরাং আত্মরক্ষার্থ চুটকি সম্বন্ধে তাঁর মতামত আমাদের পক্ষে একটু যাচিয়ে দেখা দরকার। তিনি বলেন, চুটকির একটি দোষ আছে, যখনকার তখনই, বেশি দিন থাকে না। একথা যে ঠিক নয় তা তাঁর উক্তি থেকেই প্রমাণ করা যায়। সংস্কৃত অভিধানে চুটকি শব্দ নেই, কিন্তু ওবস্তু যে সংস্কৃতসাহিত্যে আছে, সেকথা শাস্ত্রীমহাশয়ই আমাদের বলে দিয়েছেন। তাঁর মতে কালিদাস ও ভবভূতির পর চুটকি আরম্ভ হইয়াছিল; কেননা, শতক দশক অষ্টক সপ্তশতী এইসব তো চুটকিসংগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়। তথাস্তু। শাস্ত্রীমহাশয়ের বর্ণিত সংস্কৃত চুটকির দুটি-একটি নমুনার সাহায্যেই দেখানো যেতে পারে যে, আর্যযুগেও চুটকি কাব্যাচাৰ্যদিগের নিকট অতি উপাদেয় ও মহা বস্তু বলেই প্রতিপন্ন হত। ভর্তৃহরির শতক-তিনটি সকলের নিকটই সপরিচিত, এবং ‘গাঁথা-সপ্তশতী’ও বাংলাদেশে একেবারে অপরিচিত নয়। ভর্তৃহরি ভবভূতির পূর্ববর্তী কবি; কেননা, জনরব এই যে তিনি কালিদাসের ভ্রাতা, এবং ইতিহাসের অভাবে কিংবদন্তীই প্রামাণ্য। সে যাই হোক, গাঁথা-সপ্তশতী’ যে কালিদাসের জন্মের অন্তত দু-তিন শ বছর পূর্বে সংগৃহীত হয়েছিল, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। তাহলে দাঁড়াল এই যে, আগে আসে চুটকি তার পর আসে মহাকাব্য এবং মহানাটক। অভিব্যক্তির নৈসর্গিক নিয়মই এই যে, এ জগতে সব জিনিসই ছোট থেকে ক্রমে বড় হয়। সাহিত্যও ঐ একই নিয়মের অধীন। তার পর পূর্বোক্ত শতকত্রয় এবং পূর্বোক্ত সপ্তশতী যখনকার তখনকারই নয়, চিরদিনকারই। এ মত আমার নয়, বাণভট্টের। গাঁথাসপ্তশতী শুধু চুটকি নয় একেবারে প্রাকৃত-চুটকি, তথাপি শ্রীহর্ষকারের মতে
‘অবিনাশিনমগ্ৰাম্যমকরোৎসাতবাহনঃ।
বিশুদ্ধ জাতিভিঃ কোশং রঙ্গৈরিব সুভাষিতৈঃ॥
তারপর ভর্তৃহরি যে একন’র পান্না এক-ন’র চুনি এবং এক-ন’র নীলা–এই তিন-ন’র রত্নমালা সরস্বতীর কণ্ঠে পরিয়ে গেছেন, তার প্রতি-রত্নটি যে বিশুদ্ধজাতীয় এবং অবিনাশী, তার আর সন্দেহ নেই। যাবচ্চন্দ্রদিবাকর এই তিন শত বর্ণোজ্জল লোক সরস্বতীর মন্দির অহর্নিশি আলোকিত করে রাখবে।
আসল কথা, চুটকি যদি হয় হয়, তাহলে কাব্যের চুটকিত্ব তার আকারের উপর নয় তার প্রকারে অথবা বিকারের উপর নির্ভর করে, নচেৎ সমগ্ৰ সংস্কৃত কাব্যকে চুটকি বলতে হয়। কেননা, সংস্কৃতভাষায় চার ছত্রের বেশি কবিতা নেই কাব্যেও নয় নাটকেও নয়। শুধু কাব্য কেন, হাতে-বহরে বেদও চুটকির অন্তর্ভূত হয়ে পড়ে। শাস্ত্রমহাশয় বলেন যে, বাঙালি-ব্রাহ্মণ বুদ্ধিমান ব’লে বেদাভ্যাস করেন না। কর্ণবেধের জন্য যতটুকু বেদ দরকার, ততটুকুই এদেশে ব্রাহ্মণসন্তানের করায়ত্ত। অথচ বাঙালি বেদপাঠ না করেও একথা জানে যে, ঋক হচ্ছে ছোটকবিতা এবং সাম গান। সুতরাং আমরা যখন ছোটকবিতা ও গান রচনা কবি, তখন আমরা ভারতবর্ষের কাব্যরচনার সনাতন রীতিই অনুসরণ করি।।
শাস্ত্রীমহাশয় মুখে যাই বলুন, কাজে তিনি চুটকিরই পক্ষপাতী। তিনি আজীবন চুটকিতেই গলা সেধেছেন, চুটকিতেই হাত তৈরি করেছেন, সুতরাং কি লেখায়, কি বক্তৃতায়, আমরা তাঁর এই অভ্যস্ত বিদ্যারই পরিচয় পাই। তিনি বাঙালির যে বিংশপর্ব মহাগৌরব রচনা করেছেন, তা ঐতিহাসিক চুটকি বই আর কিছুই নয়; অন্তত সে রচনাকে শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় অন্য কোননা নামে অভিহিত করবেন না।
একথা নিশ্চিত যে, তিনি সরকারমহাশয়ের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন নি, সম্ভবত এই বিবাসে যে, বৈজ্ঞানিকপদ্ধতি অনুসারে আবিষ্কৃত সত্য বাঙালির পক্ষে পুষ্টিকর হতে পারে, কিন্তু রুচিকর হবে না। সরকারমহাশয় বলেন যে, এদেশের ইতিহাসের সত্য যতই অপ্রিয় হোক বাঙালিকে তা বলতেও হবে, শুনতেও হবে। অপরপক্ষে শাস্ত্রীমহাশয়ের উদ্দেশ্য তাঁর রচনা লোকের মুখরোচক করা, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য তিনি নানারকম সত্য ও কল্পনা একসঙ্গে মিলিয়ে ঐতিহাসিক সাড়ে-বত্রিশ-ভাজার সৃষ্টি করেছেন। ফলে এ রচনায় যে মাল আছে, তাও মশলা থেকে পথক করে নেওয়া যায় না। শাস্ত্রীমহাশয়ের কথিত বাংলার পারাবত্তের কোনো ভিত্তি আছে কি না বলা কঠিন। তবে এ ইতিহাসের যে গোড়াপত্তন করা হয় নি, সেবিষয়ে আর দ্বিমত নেই। ইতিহাসের ছবি আঁকতে হলে প্রথমে ভূগোলের জমি করতে হয়। কোনোএকটি দেশের সীমার মধ্যে কালকে আবদ্ধ না করতে পারলে সে-কালের পরিচয় দেওয়া যায় না। অসীম আকাশের জিওগ্রাফি নেই, অনন্ত কালেরও হিস্টরি নেই। কিন্তু শাস্ত্রীমহাশয় সেকালের বাঙালির পরিচয় দিতে গিয়ে সেকালের বাংলার পরিচয় দেন নি, ফলে গৌরবটা উত্তরাধিকারী-স্বত্বে আমাদের কি অপরের প্রাপ্য এবিষয়েও সন্দেহ থেকে যায়। শাস্ত্রীমহাশয়ের শক্ত হাতে পড়ে দেখতে পাচ্ছি অঙ্গ ভয়ে বঙ্গের ভিতর সেধিয়েছে; কেননা, যে ‘হস্ত্যায়বেদ’ আমাদের সর্বপ্রথম গৌরব, সে শাস্ত্র অঙ্গরাজ্যে রচিত হয়েছিল। বাংলার লম্বাচৌড়া অতীতের গণবর্ণনা করতে হলে বাংলাদেশটাকেও একটু লম্বাচৌড়া করে নিতে হয়, সম্ভবত সেইজন্য শাস্ত্রীমহাশয় আমাদের পূর্বপুরুষদের হয়ে অঙ্গকেও বেদখল করে বসেছেন। তাই যদি হয়, তাহলে বরেন্দ্রভূমিকে ছেটে দেওয়া হল কেন। শুনতে পাই, বাংলার অসংখ্য প্রত্নরাশি বরেন্দ্রভূমি নিজের বুকের ভিতর লুকিয়ে রেখেছে। বাংলার পূর্বগৌরবের পরিচয় দিতে গিয়ে বাংলার যে ভূমি সবচেয়ে প্রত্নগর্ভা, সে প্রদেশের নাম পর্যন্ত উল্লেখ না করবার কারণ কি। যদি এই হয় যে, পূর্বে উত্তরবঙ্গের আদৌ কোনো অস্তিত্ব ছিল না, এবং থাকলেও সেদেশ বঙ্গের বহির্ভূত ছিল, তাহলে সেকথাটাও বলে দেওয়া উচিত। নচেৎ বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি আমাদের মনে একটা ভুল ধারণা এমনি বদ্ধমূল করে দেবে যে, তার ‘আমল পরিবর্তন’ কোনো চুটকি ইতিহাসের দ্বারা সাধিত হবে না।
শাস্ত্রীমহাশয় যে তাম্রশাসনে শাসিত নন, তার প্রমাণ তিনি পাতায় পাতায় বলেন, ‘আমি বলি’ ‘আমার মতে’ এই সত্য। এর থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শাস্ত্রীমহাশয়ের ইতিহাস বস্তুতন্ত্রতার ধার ধারে না, অর্থাৎ এককথায় তা কাব্য; এবং যখন তা কাব্য, তখন তা যে চুটকি হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি।
শাস্ত্রীমহাশয়ের, দেখতে পাই, আর-একটি এই অভ্যাস আছে যে, তিনি নামের সাদশ্য থেকে পৃথক-পথক বস্তু এবং ব্যক্তির ঐক্য প্রমাণ করেন। একীকরণের এ পদ্ধতি অবশ্য বৈজ্ঞানিক নয়। কৃষ্ট এবং খষ্ট, এ দুটি নামের যথেষ্ট সাদশ্য থাকলেও ও দুটি অবতারের প্রভেদ শুধু বর্ণগত নয়, বগগতও বটে। কিন্তু শাস্ত্রীমহাশয়ের অবলম্বিত পদ্ধতির এই একটি মহাগুণ যে, ঐ উপায়ে অনেক পর্বগৌরব আমাদের হাতে আসে, যা বৈজ্ঞানিক হিসেবে ন্যায়ত অপরের প্রাপ্য। কিন্তু উক্ত উপায়ে অতীতকে হস্তান্তর করার ভিতর বিপদও আছে। একদিকে যেমন গৌরব আসে, অপরদিকে তেমনি অগৌরবও আসতে পারে। অগৌরব শুধু যে আসতে পারে তাই নয়, বস্তুত এসেছে।
স্বয়ং শাস্ত্রীমহাশয় ‘ঐতরেয় আরণ্যক’ হতে এই সত্য উদ্ধার করেছেন যে, প্রাচীন আর্যেরা বাঙালিজাতিকে পাখি বলে গালি দিতেন। সে বচনটি এই–
‘বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদা’
প্রথম-পরিচয়ে আর্যেরা যে বাঙালিজাতির সম্বন্ধে অনেক অকথা কুকথা বলেন, তার পরিচয় আমরা এ যুগেও পেয়েছি, vide Macaulay। সুতরাং প্রাচীন আর্যেরাও যে প্রথম-পরিচয়ে বাঙালিদের প্রতি নানারূপ কটু প্রয়োগ করেছিলেন, একথা সহজেই বিশ্বাস হয়। তবে এক্ষেত্রে এই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, যদি গালি দেওয়াই তাঁদের অভিপ্রায় ছিল, তাহলে আর্যেরা আমাদের পাখি বললেন কেন। পাখি বলে গাল দেবার প্রথা তো কোনো সভ্যসমাজে প্রচলিত দেখা যায় না। বরং বলবল’ ‘ময়না’ প্রভৃতি এদেশে আদরের ডাক বলেই গণ্য। এবং ব্যক্তিবিশেষের বুদ্ধির প্রশংসা করতে হলে আমরা তাকে ‘ঘুঘু’-উপাধিদানে সম্মানিত করি। অপমান করবার উদ্দেশ্যে মানুষকে যেসব প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে, তারা প্রায়শই ভূচর এবং চতুষ্পদ, দ্বিপদ এবং খেচর নয়। পাখি বলে নিন্দা করবার একটিমাত্র শাস্ত্রীয় উদাহরণ আমার জানা আছে। বাণভট্ট তাঁর সমসাময়িক কুকবিদের কোকিল বলে ভৎসনা করেছেন; কেননা, তারা বাচাল কামকারী এবং তাদের দৃষ্টি রাগাধিষ্ঠিত’—অর্থাৎ তাদের চক্ষু, রক্তবর্ণ। গাল হিসেবে এ যে যথেষ্ট হল না— সেকথা বাণভট্টও বুঝেছিলেন; কেননা, পরবর্তী শ্লোকেই তিনি বলেছেন যে, কুকুরের মত কবি ঘরে-ঘরে অসংখ্য মেলে, কিন্তু শরভের মত কবি মেলাই দুর্ঘট। এস্থলে কবিকে প্রশংসাচ্ছলে কেন শরভ বলা হল, একথা যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, তার উত্তর, শরভ জানোয়ার হলেও চতুষ্পদ নয়, অষ্টপদ; এবং ‘তার অতিরিক্ত চারখানি পা ভূচর নয়, খেচর।
এইসব কারণে, কেবলমাত্র শব্দের সাদশ্যে থেকে এ অনুমান করা সংগত হবে না যে, আর্যঋষিরা অপর এত কড়াকড়া গাল থাকতে আমাদের পূর্বপুরুষদের কেবলমাত্র পাখি বলে গাল দিয়েছেন। শাস্ত্রীমহাশয়ের মতে আমাদের সঙ্গে মাগধ এবং চের জাতিও এ গালির ভাগ পেয়েছে। কেননা, তাঁর মতে বঙ্গ হচ্ছে বাঙালি, বগধা হচ্ছে মগধা এবং চেরপাদা হচ্ছে চের নামক অসভ্য জাতি। ‘চেরপাদা’ যে কি করে ‘চের’তে দাঁড়াল, বোঝা কঠিন। বাক্যের পদচ্ছেদের অর্থ পা কেটে ফেলা নয়। অথচ শাস্ত্রীমহাশয় ‘চেরপাদা’র পা-দুখানি কেটে ফেলেই ‘চের’ খাড়া করেছেন।
‘বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদা’— এইযুক্তপদের, শুনতে পাই, সেকেলে পণ্ডিতেরা এইরূপ পদচ্ছেদ করেন–
বঙ্গা+অবগধাঃ+চ+ইরপাদা
ইরপাদা অর্থে সাপ। তাহলে দাঁড়াল এই যে, বাঙালি ও বেহারিকে প্রথমে পাখি এবং পরে সাপ বলা হয়েছে। উক্ত বৈদিক নিন্দার ভাগ আমি বেহারিদের দিতে পারি নে। অবগধা মানে যে মাগধ, এর কোনো প্রমাণ নেই। অতএব শাস্ত্রীমহাশয় যেমন ‘চেরপাদা’র শেষ দুই বর্ণ ছেটে দিয়ে ‘চের’ লাভ করেছেন, আমিও তেমনি ‘অবগধা’ শব্দের প্রথম দুটি বর্ণ বাদ দিয়ে পাই ‘গধা’। এইরূপ বর্ণবিচ্ছেদের ফলে উক্ত বচনের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আর্যঋষিদের মতে বাঙালি আদিতে পক্ষী, অন্তে সর্প এবং ইতিমধ্যে গর্দভ।
‘অবগধা’কে ‘গধা’য় রুপান্তরিত করা সম্বন্ধে কেউ-কেউ এই আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন যে, সেকালে যে গাধা ছিল তার কোনো প্রমাণ নেই। শাস্ত্রীমহাশয় বাঙালির প্রথম গৌরবের কারণ দেখিয়েছেন যে, পরাকালে বাংলায় হাতি ছিল, কিন্তু বাঙালির দ্বিতীয় গৌরবের এ কারণ দেখান নি যে, সেকালে এদেশে গাধাও ছিল। কিন্তু গাধা যে ছিল, এ অনুমান করা অসংগত হবে না। কেননা, যদি সেকালে গাধা না থাকত তো একালে এদেশে এত গাধা এল কোথা থেকে। ঘোড়া যে বিদেশ থেকে এসেছে, তার পরিচয় ঘোড়ার নামেই পাওয়া যায়; যথা পগেয়া ভুটিয়া তাজি আরবি ইত্যাদি। কিন্তু গর্দভদের এরূপ কোনো নামরূপের প্রভেদ দেখা যায় না। এবং ও জাতি যে যে-কোনো অর্বাচীন যুগে বঙ্গদেশে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছে, তারও কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে, রাসভকুল অপর সকল দেশের ন্যায় এদেশে এখনও আছে, পূর্বেও ছিল। তবে একমাত্র নামের সাদশ্য থেকে এরূপ অনুমান করা অসংগত হবে যে, আর্যঋষিরা পুরাকালের বাঙালিদের এরূপ তিরস্কারে পুরস্কৃত করেছেন। সংস্কৃতভাষায় ‘বঙ্গ’ শব্দের অর্থ বক্ষ। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, আরণ্যকশাস্ত্রে বক্ষ পক্ষী সর্প প্রভৃতি আরণ্য জীবজন্তুরই উল্লেখ করা হয়েছে, বাঙালির নামও করা হয় নি। অতএব আমাদের অতীত অতি গৌরবেরও বস্তু নয়, অতি অগৌরবেরও বস্তু নয়।।
আর-একটি কথা। হীরেন্দ্রবাবু দর্শন-শব্দের, এবং যোগেশবাবু বিজ্ঞানশব্দের নিরুক্তের আলোচনা করেছেন, কিন্তু যদুবাবু ইতিহাসের নিরুক্ত সম্বন্ধে নীরব। ইতিহাস-শব্দ সম্ভবত হস্ ধাতু হতে উৎপন্ন, অন্তত শাস্ত্রীমহাশয়ের ইতিহাস যে হাস্যরসের উদ্রেক করে, সেবিষয়ে আর-কোনো সন্দেহ নেই। এমনকি, আমার সময়ে সময়ে মনে হয় যে, শাস্ত্রীমহাশয় পুরাতত্ত্বের ছলে আত্মশ্লাঘাপরায়ণ বাঙালিজাতির সঙ্গে একটি মস্ত রসিকতা করেছেন।
জ্যৈষ্ঠ ১৩২২
টীকা ও টিপ্পনি
শ্ৰীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় সম্প্রতি দুঃখ করে বলেছেন যে, সেকালে সবে তিন-চারখানি মাসিকপত্র ছিল এবং তার একখানিও মাসে-মাসে বেরত না; থেকে-থেকেই তার একটি-না-একটি বিনা-নোটিশে বন্ধ হয়ে যেত।
এ দুঃখ আমাদের নেই। একালে অন্তত এমন ত্রিশ-চল্লিশখানি মাসিকপত্র আছে যা মাসে-মাসে বেরয়, আর তার একখানিও বন্ধ হয়ে যায় না।
শাস্ত্রে বলে ‘অধিকন্তু ন দোষায়’, ইংরেজিতে বলে ‘The more the merrier’। সুতরাং পর্ব-পশ্চিম যেদিক থেকেই দেখ, মাসিকপত্রের এই আধিক্যে আমাদের খুশি হবারই কথা।
তবে মাসিকপত্রের অতিবাড়বাড়াটা সাহিত্যের পক্ষে কল্যাণকর কি অকল্যাণকর, সেবিষয়ে সকলে একমত নন। স্বনামধন্য ইংরেজ লেখক অস্কার ওআইল্ডের মতে সাহিত্য এবং সাময়িক-সাহিত্য, এ দুয়ের ভিতর একটা স্পষ্ট প্রভেদ আছে। তিনি বলেন, Literature is not read এবং Journalism is unreadable
পূর্বোক্ত বচনের প্রথমাংশ যে অনেক পরিমাণে সত্য, সেকথা আমরা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য। চণ্ডীদাস থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যেসকল লেখক নিয়ে আমরা মহা গৌরব করি, তাঁদের রচিত কাব্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে যাঁর পরিচয় আছে–এমন সাহিত্যিক শতেকে জনেক মেলে কি না, সেবিষয়ে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে।
‘লাখে না মিলল এক’–এ দুঃখের কথা, আমার বিশ্বাস, বিদ্যাপতিঠাকুর ভবিষ্যৎ-পাঠকসমাজের প্রতি লক্ষ্য করেই বলেছেন। তার পর রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে সকল সমালোচকের যে পরিচয় নেই, এর প্রমাণ আমি সম্প্রতি পেয়েছি। বঙ্গসরস্বতীর জনৈক ধনাঢ্য পণ্ঠপোষক সম্প্রতি কলিকাতার সাহিত্যসভায় এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষার দৈন্য এবং ভাবের দৈন্য গোপন করবার জন্যই মৌখিকভাষার আশ্রয় অবলম্বন করেছেন। একথা বলাও যা, আর দুয়ে-দয়ে পাঁচ করবার অক্ষমতা বশতই শ্রীযুক্ত পরাঞ্জপে দুয়ে-দয়ে চার করেন একথা বলাও তাই।
সরস্বতীর পঠপোষক হবার জন্য অবশ্য কারও তাঁর মুখদর্শন করবার কোনো দরকার নেই। তবে উক্ত সভাস্থ সমবেত বিদ্যণ্ডলী যে পূর্বোক্ত অত্যুক্তির কোনো প্রতিবাদ করেন নি, তার থেকে অনুমান করা অসংগত হবে না যে, রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সঙ্গে সাহিত্যিক সভ্যদের কারও বিশেষ পরিচয় নেই। না-পড়ে-পণ্ডিত হওয়ায় বাঙালি তো তার অসাধারণ বুদ্ধিরই পরিচয় দেয়।
না-পড়ে-পশ্চিত হওয়া সম্ভব হলেও না-লিখে-লেখক হওয়া যায় কি না সেবিষয়ে আমার সন্দেহ আছে, এবং সেইজন্যই মাসিকপত্রের বংশবৃদ্ধিটি সুখের কিংবা দুঃখের বিষয়, সেবিষয়ে আমি মনস্থির করে উঠতে পারি নি।
সাময়িক সাহিত্য যে অপাঠ্য, অস্কার ওআইল্ডের এ মত আমাদের গ্রাহ্য করবার দরকার নেই। মাসিক সাপ্তাহিক এবং দৈনিক পত্র সম্বন্ধে অস্কার ওআইল্ড যে মত প্রকাশ করেছেন, তাঁর চাইতে ঢের বড় লেখক চার্লস ল্যাম, সাহিত্য সম্বন্ধে সেই একই মত প্রকারান্তরে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ‘একখানি নতুন বই প্রকাশিত হলে একখানি পরেনো বই প’ড়ো’। এর থেকে বোঝা যায় যে, সেকালের মায়ায় আমরা স্বকালের মর্যাদা বুঝতে পারি নে। কারও-কারও মতে নবসাহিত্য রচনা করা আর সরস্বতীর শ্রাদ্ধ করা একই কথা— তা মাসিকই হোক, আর সাংবৎসরিকই হোক।
তবে বইয়ের সঙ্গে মাসিকপত্রের যে একটা প্রভেদ আছে, তা আমরা সকলেই মানতে বাধ্য। বই লেখে একজনে, আর মাসিকপত্র অনেকে মিলে। এককথায়, মাসিকপত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে সরস্বতীর বারোয়ারি পুজো করা। কাজেই ব্যাপারটা অনেক সময়ে গোলে-হরিবোলে পরিণত হয়। তার পর, যেখানে চাঁদা করে কার্য উদ্ধার করতে হয়, সেখানে জাতবিচার করা চলে না— ব্রাহণ শুদ্র সকলের পক্ষে সে উৎসবে যোগদান করবার সমান, অধিকার আছে। গোল তো এই নিয়েই।
সকলে কথা কইতে পারলেও যে গান গাইতে পারে না, হাঁটতে পারলেও যে নাচতে পারে না, একথা সকলেই জানেন এবং সকলেই মানেন। কিন্তু অনেকে লিখতে পারলেও যে লিখতে পারে না, এ জ্ঞান আমরা হারিয়ে বসে আছি।
‘হারিয়ে বসে আছি’ বলবার কারণ এই যে, সংগীতের মত লেখাজিনিসটেও যে একটি আর্ট, এ জ্ঞান আমাদের পূর্বপরিষদের ছিল। সকল আলংকারিক একবাক্যে বলে গেছেন যে, কাব্যরচনা করবার জন্য দুটি জিনিস চাই–প্রথমত, প্রাক্তন সংস্কার; দ্বিতীয়ত, শিক্ষা।
একালের অনেক লেখকের বিশ্বাস যে, সাহিত্যিক হবার জন্য একমাত্র প্রাক্তন সংস্কারই যথেষ্ট, শিক্ষা-দীক্ষার কোনোরূপ আবশ্যক নেই; কেননা, তাঁদের লেখা পড়ে বোঝা যায় না, তাঁরা তাঁদের নৈসর্গিকী প্রতিভা ব্যতীত অপর কিসের উপর নির্ভর করেন। মহর্ষি চরকের শিষ্য অগ্নিবেশ বলেছেন যে, যেসকল চিকিৎসকের গুরুর নাম কেউ জানে না, যাঁদের কোনো সতীর্থ নেই, তাঁরা ‘দ্বিজিহ্ব বায়ু-ভক্ষকাঃ’। এই শ্রেণীর সাহিত্যচিকিৎসকের দল যে ক্রমে বুদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে, সেবিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই; এবং মাসিকপত্ৰসকল এই শ্রেণীর সাহিত্যিকদের প্রশ্রয় দিতে বাধ্য।
বাংলাদেশে আজকাল যদিও বা লেখক থাকে তো লেখবার বিষয় বড়একটা নেই। লেখবার সামগ্রীর যে অনটন ঘটেছে তার প্রমাণ, আজকাল কি লেখা উচিত, কি ভাষায় লেখা উচিত, কি ধরনে লেখা উচিত— এইসব নিয়ে সকলে মহা গণ্ডগোল বাধিয়েছেন। কি শহরে, কি পাড়াগাঁয়ে, এমন মাসিকপত্র নেই, যা এই পণ্ডিতের বিচারে যোগদান করে নি।
এসকল তর্কবিতর্কের যে কোনো সার্থকতা নেই, একথা আমার মুখে শোভা পায় না। তবে এইসব আলংকারিক-তত্ত্ব নিয়ে এতটা দেশজোড়া আন্দোলন হওয়াটাই আক্ষেপের বিষয়। কেননা, এসব সমস্যার বিচার করতে হলে, প্রথমত, সে বিচার করবার শিক্ষা এবং শক্তি থাকা আবশ্যক; দ্বিতীয়ত, যুক্তিযুক্ত তর্ক করবার অভ্যাস থাকা আবশ্যক।
কিন্তু ঘটনা হয়েছে অন্যরপ। নিত্যই দেখতে পাই যে, যাঁরা দু ছত্র সোজা করে লিখতে পারেন না, তাঁরাও রচনারীতি নিয়ে মন্ত-মস্ত আঁকাবাঁকা প্রবন্ধ লেখেন। তার পর দেখতে পাই, এইসব লেখকদের ধৈর্যের অপেক্ষা বীর্য ঢের বেশি। এরা যুক্তিতকের ধার ধারেন না–উপদেশ দেন, আদেশ করেন। সম্ভবত এদের বিশবাস যে, রাগের মাথায় যেকথা বলা যায়, তা সত্য হতে বাধ্য। এরা ভুলে যান যে, ক্রোধান্ধ হলে মানুষের দিগবিদিক-জ্ঞান থাকে না।
ফলে, এরা সাহিত্যের যেসব ইটপাটকেল কুড়িয়ে পান তা মাতৃভাষার উপর নিক্ষেপ করতে শুরু করেছেন। আমার সম্মুখে তিনখানি মাসিকপত্র খোলা রয়েছে; তার একখানিতে মাতৃভাষাকে ‘কিষ্কিন্ধ্যার ভাষা [সাহিত্যসংহিতা], আর-একখানিতে ‘পেত্নিভাষা’ [ভারতী], আর-একখানিতে ‘চণ্ডালীভাষা’ (উপাসনা] বলা হয়েছে। এরকম কথা যাঁরা মুখে আনতে পারেন, তাঁদের কথার প্রতিবাদ করা অসম্ভব ও নিষ্প্রয়োজন; কেননা, তাঁরা যে বঙ্গসরস্বতীর কতদূর সুসন্তান, তার পরিচয় নিজমখেই দেন। কিন্তু আমাদের মাসিকপত্রসকল যে এইসব অকথা কুকথা প্রচারের সহায়তা করেন তার থেকে বোঝ যায় যে, বাংলার বন্দেমাতরম,-যুগ চলে গিয়েছে।
আমাদের লেখবার বিষয় যে বড়-একটা নেই, তার অপর প্রমাণ— বাংলা মাসিকে প্রত্নতত্ত্বের প্রাধান্য। প্রত্নতত্ত্ব আর-যাই হোক, সাহিত্য নয়। ও বস্তু মূল্যবান, এই হিসেবেই যদি প্রত্নতত্ত্বকে মাসিকপত্রে স্থান দেওয়া হয় তাহলে রত্নতত্ত্বই বা বাদ যায় কেন। তবে যদি সম্পাদকমহাশয়েরা বলেন, বাংলার সাহিত্যওয়ালাদের মধ্যে কোনো জরি নেই, তাহলে অবশ্য আমাদের নিরুত্তর থাকতে হবে।
মাসিক সাহিত্যের প্রধান সম্বল হচ্ছে ছোটগল্প। এই ছোটগল্প কিভাবে লেখা উচিত, সেবিষয়েও আজকাল আলোচনা শুরু হয়েছে। এও আর-একটি প্রমাণ যে, লেখবার বিষয়ের অভাববশতই লেখবার পদ্ধতির বিচারই আমাদের দায়ে পড়ে করতে হয়।
এসম্বন্ধে আমার দুটি কথা বলবার আছে। আমার মতে ছোটগল্প প্রথমে গল্প হওয়া চাই, তার পরে ছোট হওয়া চাই; এ ছাড়া আর-কিছুই হওয়া চাই নে।
যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে গল্প কাকে বলে, তার উত্তর ‘লোকে যা শুনতে ভালোবাসে’। আর যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন ‘ছোট’ কাকে বলে, তার উত্তর যা বড় নয়।
এর উত্তরে পাঠক আপত্তি করতে পারেন যে ডেফিনিশনটি তেমন পরিষ্কার হল না। এস্থলে আমি ছোটগল্পের তত্ত্ব নির্ণয় করবার চেষ্টা করছি। এবং আশা করি সকলে মনে রাখবেন যে তত্ত্বকথা এর চাইতে আর পরিষ্কার হয় না। এর জন্য দুঃখ করবারও কোনো কারণ নেই; কেননা, সাহিত্যের তত্ত্বজ্ঞানের সাহায্যে সাহিত্যরচনা করা যায় না। আগে আসে বস্তু, তার পরে তার তত্ত্ব। শেষটি না থাকলেও চলে, কিন্তু প্রথমটি না থাকলে সাহিত্যজগৎ শুন্য হয়ে যায়। এ বিপদ যে সম্মুখে নেই, তাও ভরসা করে বলা চলে না। কেননা, মাসিকপত্রে লেখবার লোক অনেক থাকলেও তাঁদের লেখবার বিষয় অনেক নেই; আর লেখবার বিষয় অনেক থাকলেও তা লেখবার অনেক লোক নেই। ফলকথা, সাহিত্যের প্রবৃদ্ধি হয় যোগে, আর তার শ্রীবৃদ্ধি হয় গুণে।
শ্রাবণ ১৩২৩
তরজমা
আমরা ইংরেজজাতিকে কতকটা জানি, এবং আমাদের বিশ্বাস যে, প্রাচীন হিন্দুজাতিকে তার চাইতেও বেশি জানি; আমরা চিনি নে শুধু নিজেদের।
আমরা নিজেদের চেনবার কোনো চেষ্টাও করি নে, কারণ আমাদের বিশ্বাস যে, সে জানার কোনো ফল নেই; তা ছাড়া নিজেদের ভিতর জানবার মত কোনো পদার্থ আছে কি না, সে বিষয়েও অনেকের সন্দেহ আছে।
বাঙালির নিজস্ব বলে মনে কিংবা চরিত্রে যদি কোনো পদার্থ থাকে, তাকে আমরা ডরাই; তাই চোখের আড়াল করে রাখতে চাই। আমাদের ধারণা যে, বাঙালি তার বাঙালিত্ব না হারালে আর মানুষ হয় না। অবশ্য অপরের কাছে তিরস্কৃত হলে আমরা রাগ করে ঘরের ভাত (যদি থাকে ততো) বেশি করে খাই; কিন্তু উপেক্ষিত হলেই আমরা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হই। মান এবং অভিমান এক জিনিস নয়। প্রথমটির অভাব হতেই দ্বিতীয়টি জন্মলাভ করে।
আমরা যে নিজেদের মান্য করি নে, তার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, আমরা উন্নতি অর্থে বুঝি— হয় বতমান ইউরোপের দিকে এগনো, নয় অতীত ভারতবর্ষের দিকে পিছননা। আমরা নিজের পথ জানি নে বলে আজও মনঃস্থির করে উঠতে পারি নি যে, পর্ব এবং পশ্চিম এই দুটির মধ্যে কোন, দিক অবলম্বন করলে আমরা ঠিক গন্তব্য স্থানে গিয়ে পৌঁছব। কাজেই আমরা ইউরোপীয় সভ্যতার দিকে তিন-পা এগিয়ে আবার ভারতবর্ষের দিকে দু-পা পিছিয়ে আসি, আবার অগ্রসর হই, আবার পিছ, হটি। এই কুর্নিশ করাটাই আমাদের নব-সভ্যতার ধর্ম ও কর্ম।
উক্ত ক্রিয়াটি আমাদের পক্ষে বিশেষ গৌরবসচক না হলেও মেনে নিতে হবে। যা মনে সত্য বলে জানি, সেসম্বন্ধে মনকে চোখ ঠেরে কোনো লাভ নেই। আমরা দোটানার ভিতর পড়েছি–এই সত্যটি সহজে স্বীকার করে নিলে আমাদের উন্নতির পথ পরিষ্কার হয়ে আসবে। যা আজ উভয়সংকট বলে মনে হচ্ছে, তাই আমাদের উন্নতির স্রোতকে একটি নির্দিষ্ট পথে বদ্ধ রাখবার উভয়কল বলে বুঝতে পারব। আমরা যদি চলতে চাই তো আমাদের একল-ওকল দু কল রক্ষা করেই চলতে হবে।
আমরা স্পষ্ট জানি আর না-জানি, আমরা এই উভয়কল অবলম্বন করেই চলবার চেষ্টা করছি। সকল দেশেরই সকল যুগের একটি বিশেষ ধর্ম আছে। সেই যুগধর্ম অনুসারে চলতে পারলেই মানুষ সার্থকতা লাভ করে। আমাদের এ যুগে সত্যযুগও নয় কলিযুগ নয়— শুধু তরজমার যুগ। আমরা শুধু কথায় নয়, কাজেও একেলে বিদেশী এবং সেকেলে স্বদেশী সভ্যতার অনুবাদ করেই দিন কাটাই। আমাদের মুখের প্রতিবাদও ঐ একই লক্ষণাক্রান্ত। আমরা সংস্কৃতের অনুবাদ করে নূতনের প্রতিবাদ করি, এবং ইংরেজির অনুবাদ করে পুরাতনের প্রতিবাদ করি। আসলে রাজনীতি সমাজনীতি ধর্ম শিক্ষা সাহিত্য সকল ক্ষেত্রেই তরজমা করা ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর নেই। সুতরাং আমাদের বর্তমান যুগটি তরজমার যুগ বলে গ্রাহ্য করে নিয়ে ঐ অনুবাদ-কাটি ষোলোআনা ভালোরকম করার উপর আমাদের পুরুষার্থ এবং কৃতিত্ব নির্ভর করছে।
পরের জিনিসকে আপনার করে নেবার নামই তরজমা। সুতরাং ও কার্য করাতে আমাদের কোনো ক্ষতি নেই, এবং নিজেদের দৈনন্যর পরিচয় দেওয়া হয় মনে করেও লজ্জিত হবার কারণ নেই। কেননা, নিজের ঐশ্বর্য না থাকলে লোকে যেমন দান করতে পারে না, তেমনি নেবার যথেষ্ট ক্ষমতা না থাকলে লোকে গ্রহণও করতে পারে না। স্মৃতির মতে, দাতা এবং গ্রহীতার পরস্পর যোগ না হলে দানক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। একথা সম্পর্ণে সত্য। মত ব্যক্তি দাতাও হতে পারে না, গ্রহীতাও হতে পারে না; কারণ দান এবং গ্রহণ উভয়ই জীবনের ধর্ম। বুদ্ধদেব যিশুখৃস্ট মহম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষদের নিকট কোটি-কোটি মানব ধর্মের জন্য ঋণী। কিন্তু তাঁদের দত্ত অমূল্য রত্ন তাঁদের হাত থেকে গ্রহণ করবার ক্ষমতা কেবলমাত্র তাঁদের সমকালবর্তী জনকতক মহাপুরুষেরই ছিল। এবং শিষ্যপরম্পরায় তাঁদের মত আজ লক্ষ লক্ষ লোকের ঘরের সামগ্রী হয়ে উঠেছে। পৃথিবীতে গর, হওয়া বেশি শক্ত, কিংবা শিষ্য হওয়া বেশি শক্ত, বলা কঠিন। যাঁদের বেদান্তশাস্ত্রের সঙ্গে স্বল্পমাত্রও পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন যে, পরাকালে গররা কাউকে ব্রহনবিদ্যা দান করবার পূর্বে শিষ্যের সে বিদ্যা গ্রহণ করবার উপযোগিতা সম্বন্ধে কিরূপ কঠিন পরীক্ষা করতেন। উপনিষদকে গুহ্যশাস্ত্র করে রাখবার উদ্দেশ্যই এই যে, যাদের শিষ্য হবার সামথ্য নেই, এমন লোকেরা ব্রহ্মবিদ্যা নিয়ে বিদ্যে ফলাতে না পারে। একথা সম্পূর্ণ সত্য যে, শক্তিমান গর, হবার একমাত্র উপায় পূর্বে ভক্তিমান শিষ্য হওয়া। বর্তমান যুগে আমরা ভক্তি-পদার্থটি ভুলে গেছি, আমাদের মনে আছে শুধু অভক্তি ও অতিভক্তি। এ দুয়ের একটিও সাধুতার লক্ষণ নয়, তাই ইংরেজি-শিক্ষিত লোকের পক্ষে অপর কাউকে শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব।
আমরা কথায় বলি, জ্ঞানলাভ করি; কিন্তু আসলে জ্ঞান উত্তরাধিকারীসত্ত্বে কিংবা প্রসাদস্বরূপে লাভ করবার পদার্থ নয়। আমরা সজ্ঞানে জন্মলাভ করি নে, কেবল জ্ঞান অর্জন করবার ক্ষমতামাত্র নিয়ে ভূমিষ্ঠ হই। জানাব্যাপারটি মানসিক চেষ্টার অধীন, জ্ঞান একটি মানসিক ক্রিয়া মাত্র; এবং সে ক্রিয়া ইচ্ছাশক্তির একটি বিশেষ বিকাশ। মন-পদার্থটি একটি বেওয়ারিশ প্লেট নয়, যার উপর বাহ্যজগত্রপে পেনসিল শুধু হিজিবিজি কেটে যায়; অথবা ফোটোগ্রাফিক প্লেটও নয়, যা কোনোরূপ অন্তর্গঢ় রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা বাহ্যজগতের ছায়া ধরে রাখে। যে প্রক্রিয়ার বলে আমরা জ্ঞাতব্য বিষয়কে নিজের ইচ্ছা এবং ক্ষমতা অনুসারে নিজের অন্তর্ভুত করে নিতে পারি, তারই নাম জ্ঞান। আমরা মনে-মনে যা তরজমা করে নিতে পারি, তাই আমরা যথার্থ জানি; যা পারি নে, তার শুধু নামমাত্রের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। ঐ তরজমা করার শক্তির উপরই মানুষের মনুষ্যত্ব নির্ভর করে। সুতরাং একাগ্রভাবে তরজমা-কার্যে ব্রতী হওয়াতে আমাদের পুরুষকার বৃদ্ধি পাবে বই ক্ষীণ হবে না।
আমি পূর্বে বলেছি যে, আমরা সকলে মিলে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই, হয় ইউরোপীয় নয় আর্য সভ্যতার তরজমা করবার চেষ্টা করছি, কিন্তু ফলে আমরা তরজমা না করে শুধু নকলই করছি। নকল করার মধ্যে কোনোরূপ গৌরব বা মনুষ্যত্ব নেই। মানসিক শক্তির অভাববশতই মানুষে যখন কোনো জিনিস রপান্তরিত করে নিজের জীবনের উপযোগী করে নিতে পারে না, অথচ লোভবশত লাভ করতে চায়, তখন তার নকল করে। নকলে বাইরের পদার্থ বাইরেই থাকে, আমাদের অন্তর্ভূত হয় না; তার দ্বারা আমাদের মনের এবং চরিত্রের কান্তি পুষ্ট হয় না, ফলে মানসিক শক্তির যথেষ্ট চর্চার অভাববশত দিন-দিন সে শক্তি হ্রাস হতে থাকে। ইউরোপীয় সভ্যতা আমরা নিজেদের চারিপাশে জড়ো করেও সেটিকে অন্তরঙ্গ করতে পারি নি; তার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, আমরা মাঝেমাঝে সেটিকে ঝেড়ে ফেলবার জন্য ছটফট করি। মানুষে যা আত্মসাৎ করতে পারে না তাই ভস্মসাৎ করতে চায়। আমরা মুখে যাই বলি নে কেন, কাজে পব-সভ্যতা নয়, পশ্চিম-সভ্যতারই নকল করি; তার কারণ ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের চোখের সম্মুখে সশরীরে বর্তমান, অপরপক্ষে আর্য সভ্যতার প্রেতাত্মামাত্র অবশিষ্ট। প্রেতাত্মাকে আয়ত্ত করতে হলে বহু সাধনার আবশ্যক। তাছাড়া প্রেতাত্মা নিয়ে যাঁরা কারবার করেন তাঁরা সকলেই জানেন যে, দেহমুক্ত আত্মার সম্পর্কে আসতে হলে অপর-একটি দেহতে তাকে আশ্রয় দেওয়া চাই; একটি প্রাণীর মধ্যস্থতা ব্যতীত প্রেতাত্মা আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন না। আমাদের সমাজের প্রাচীন দেহ আছে বটে, কিন্তু প্রাণ নেই। শব প্রেতাত্মা কর্তৃক আবিষ্ট হলে মানুষ হয় না, বেতাল হয়। বেতাল-সিদ্ধ হবার দুরাশা খুব কম লোকেই রাখে; কাজেই শুধু মন নয়, পঞ্চেন্দ্রিয়ারা গ্রাহ্য যে ইউরোপীয় সভ্যতা আমাদের প্রত্যক্ষ রয়েছে, সাধারণত লোকে তারই অনুকরণ করে। অনুকরণ ত্যাগ করে যদি আমরা এই নব-সভ্যতার অনুবাদ করতে পারি, তাহলেই সে সভ্যতা নিজস্ব হয়ে উঠবে, এবং ঐ ক্রিয়ার সাহায্যেই আমরা নিজেদের প্রাণের পরিচয় পাব, এবং বাঙালির বাঙালিত্ব ফুটিয়ে তুলব।
তরজমার আবশ্যকত্ব স্থাপনা করে এখন কি উপায়ে আমরা সেবিষয়ে কৃতকার্য হব সেসম্বন্ধে আমার দু-চারটি কথা বলবার আছে।
সাধারণত লোকের বিশ্বাস যে, কথার চাইতে কাজ শ্রেষ্ঠ। এ বিশ্বাস বৈষয়িক হিসাবে সত্য এবং আধ্যাত্মিক হিসাবে মিথ্যা। মানুষমাত্রেই নৈসর্গিক প্রবত্তির বলে সংসারযাত্রার উপযোগী সকল কার্য করতে পারে; কিন্তু তার অতিরিক্ত কর্ম-যার ফল একে নয় দশে লাভ করে, তা-করবার জন্য মনোবল আবশ্যক। সমাজে সাহিত্যে যা-কিছু মহকার্য অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার মূলে মন-পদার্থটি বিদ্যমান। যা মনে ধরা পড়ে তাই প্রথমে কথায় প্রকাশ পায়, সেইকথা অবশেষে কার্যরূপে পরিণত হয়; কথার সক্ষশরীর কার্যরপ স্থূলদেহ ধারণ করে। আগে দেহটি গড়ে নিয়ে, পরে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টাটি একেবারেই বৃথা। কিন্তু আমরা রাজনীতি সমাজনীতি ধর্ম সাহিত্য সকল ক্ষেত্রেই ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণের সন্ধান না করে শুধু তার দেহটি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করায় নিত্যই ইতোনষ্টস্ততেভ্রষ্ট হচ্ছি। প্রাণ নিজের দেহ নিজের রূপ নিজেই গড়ে নেয়। নিজের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির বলেই বীজ ক্রমে বক্ষ-রূপ ধারণ করে। সুতরাং আমরা যদি ইউরোপীয় সভ্যতার প্রাণে প্রাণবন্ত হয়ে উঠতে পারি, তাহলেই আমাদের সমাজ নবকবের ধারণ করবে। এই নবসভ্যতাকে মনে সম্পূর্ণরূপ পরিপাক করতে পারলেই আমাদের কান্তি পুষ্ট হবে। কিন্তু যতদিন সে সভ্যতা আমাদের মুখস্থ থাকবে কিন্তু উদরস্থ হবে না, ততদিন তার কোনো অংশই আমরা জীর্ণ করতে পারব না। আমরা যে, ইউরোপীয় সভ্যতা কথাতেও তরজমা করতে পারি নি, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, আমাদের নূতন শিক্ষালব্ধ মনোভাবসকল শিক্ষিত লোকদেরই রসনা আশ্রয় করে রয়েছে, সমগ্র জাতির মনে স্থান পায় নি। আমরা ইংরেজি ভাব ভাষায় তরজমা করতে পারি নে বলেই আমাদের কথা দেশের লোকে বোঝে না, বোঝে শুধু ইংরেজি-শিক্ষিত লোকে। এদেশের জনসাধারণের নেবার ক্ষমতা কিছু কম নয়, কিন্তু আমাদের কাছ থেকে তারা যে কিছু, পায় না, তার একমাত্র কারণ আমাদের অন্যকে দেবার মত কিছু নেই; আমাদের নিজস্ব বলে কোনো পদার্থ নেই–আমরা পরের সোনা কানে দিয়ে অহংকারে মাটিতে পা দিই নে। অপরপক্ষে আমাদের পবিপুরুষদের দেবার মত ধন ছিল, তাই তাঁদের মনোভাব নিয়ে আজও সমগ্র জাতি ধনী হয়ে আছে। ঋষিবাক্যসকল লোকমুখে এমনি সুন্দর ভাবে তরজমা হয়ে গেছে যে, তা আর তরজমা বলে কেউ বুঝতে পারেন না। এদেশের অশিক্ষিত লোকের রচিত বাউলের গান কাউকে আর উপনিষদের ভাষায় অনুবাদ করে বোঝাতে হয় না, অথচ একই মনোভাব ভাষান্তরে বাউলের গানে এবং উপনিষদে দেখা দেয়। আত্মা যেমন এক দেহ ত্যাগ করে অপর দেহ গ্রহণ করলে পবদেহের অতিমাত্রও রক্ষা করে না, মনোভাবও যদি তেমনি এক ভাষার দেহত্যাগ করে অপর-একটি ভাষার দেহ অবলম্বন করে, তাহলেই সেটি যথার্থ অনুদিত হয়।
উপযুক্ত তরজমার গুণেই বৈদান্তিক মনোেভাবসকল হিন্দুসন্তানমাত্রেরই মনে অল্পবিস্তর জড়িয়ে আছে। এদেশে এমন লোক বোধ হয় নেই, যার মনটিকে নিংড়ে নিলে অন্তত এক ফোঁটাও গৈরিক রং না পাওয়া যায়। আর্যসভ্যতার প্রেতাত্মা উদ্ধার করবার চেষ্টাটা একেবারেই অনর্থক, কারণ তার আত্মাটি আমাদের দেহাভ্যন্তরে সষপ্ত অবস্থায় রয়েছে, যদি আবশ্যক হয় ততা সেটিকে সহজেই জাগিয়ে নেওয়া যেতে পারে। ঠিক কথাটি বলতে পারলে অপরের মনের বার আরব্য-উপন্যাসের দস্যদের ধনভাণ্ডারের বারের মত আপনি খুলে যায়। আমরা, ইংরেজি-শিক্ষিত লোকেরা, জনসাধারণের মনের দ্বার খোলবার সংকেত জানি নে, কারণ আমরা তা জানবার চেষ্টাও করি নে। যেসকল কথা আমাদের মুখের উপর আলগা হয়ে রয়েছে কিন্তু মনে প্রবেশ করে নি, সেগুলি আমাদের মুখ থেকে খসে পড়লেই যে অপরের অতরে প্রবেশ লাভ করবে, এ আশা বৃথা।
আমরা যে আমাদের শিক্ষালব্ধ ভাবগলি তরজমা করতে অকৃতকার্য হয়েছি, তার প্রমাণ তো সাহিত্যে এবং রাজনীতিতে দু বেলাই পাওয়া যায়। যেমন সংস্কৃত-নাটকের প্রাকৃত সংস্কৃত-ছায়া’র সাহায্য ব্যতীত বুঝতে পারা যায় না, তেমনি আমাদের নব-সাহিত্যের কৃত্রিম প্রাকৃত ইংরেজি-ছায়ার সাহায্য ব্যতীত বোঝা যায় না। সমাজে না হোক, সাহিত্যে ‘চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা। কিন্তু আমাদের নব-সাহিত্যের বস্তু যে চোরাই-মাল, তা ইংরেজি-সাহিত্যের পাঠকমাত্রেরই কাছে ধরা পড়ে। আমরা ইংরেজিসাহিত্যের সোনারপো যা চুরি করি, তা গলিয়ে নিতেও শিখি নি। এই তো গেল সাহিত্যের কথা। রাজনীতি-বিষয়ে আমাদের সকল ব্যাপার যে আগাগোড়াই নকল, এবিষয়ে বোধ হয় আর দুমত নেই, সুতরাং সেসম্বন্ধে বেশি কিছু বলা নিতান্তই নিষ্প্রয়োজন।
আমাদের মনে-মনে বিশ্বাস যে, ধর্ম এবং দর্শন এই দুটি জিনিস আমাদের একচেটে; এবং অন্য কোনো বিষয়ে না হোক, এই দুই বিষয়ে আমাদের সহজ কৃতিত্ব কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। ইংরেজি-শিক্ষিত ভারতবাসীদের এ বিশ্বাস যে সম্পূর্ণ অমূলক, তার প্রমাণস্বরূপ দেখানো যেতে পারে যে, ঐ শ্রেণীর লোকের হাতে মনুর ধর্ম রিলিজিঅন হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ ভুল তরজমার বলে ব্যবহারশাস্ত্র আধ্যাত্মিক ব্যাপার হয়ে উঠেছে। মশাস্ত্র এবং মোক্ষশাস্ত্রের ভেদজ্ঞান আমাদের সস্ত হয়েছে। ধমের অর্থ ধরে রাখা এবং মোক্ষের অর্থ ছেড়ে দেওয়া, সুতরাং এ দুয়ের কাজ যে এক নয়, তা শুধু ইংরেজিনবিশ আর্য-সন্তানরাই বুঝতে পারেন না।
গীতা আমাদের হাতে পড়বামাত্র তার হরিভক্তি উড়ে যায়। সেই কারণে শ্ৰীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ‘গীতায় ঈশ্বরবাদ’এর প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে নব্য পণ্ডিতসমাজে শুধু বিবাদবিসম্বাদের সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর গীতার কম ইংরেজি work-রূপ ধারণ করে আমাদের কাছে গ্রাহ্য হয়েছে; অর্থাৎ কর্মকাণ্ডের কর্ম কাণ্ডহীন হয়েই আমাদের কাছে উচ্চ বলে গণ্য হয়েছে। এই ভুল তরজমার প্রসাদেই, যে কমের উদ্দেশ্য পরের হিত এবং নিজের আত্মার উন্নতিসাধন পরলোকের অভ্যুদয়ও নয়, সেই কর্ম আজকাল ইহলোকের অ্যুদয়ের জন্য ধর্ম বলে গ্রাহ্য হয়েছে। যে কাজ মানুষে পেটের দায়ে নিত্য করে থাকে, তা করা কর্তব্য–এইটকু শেখাবার জন্য ভগবানের যে লোগায়তন দেহ ধারণ করে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হবার আবশ্যকতা ছিল না— এ সোজা কথাটাও আমরা বুঝতে পারি নে। ফলে আমাদের-কৃত গীতার অনুবাদ বক্তৃতাতেই চলে, জীবনে কোনো কাজে লাগে না।
একদিকে আমরা এদেশের প্রাচীন মতগলিকে যেমন ইংরেজি পোশাক পরিয়ে তার চেহারা বিলকুল বদলে দিই, তেমনি অপরদিকে ইউরোপীয় দর্শন-বিজ্ঞানকেও আমরা সংস্কৃতভাষার ছদ্মবেশ পরিয়ে লোকসমাজে বার করি।
নিত্যই দেখতে পাই যে, খাঁটি জমান মাল স্বদেশী বলে পাঁচজনে সাহিত্যের বাজারে কাটাতে চেষ্টা করছে। হেগেলের দর্শন শংকরের নামে বেনামি করে অনেকে কতক পরিমাণে অজ্ঞ লোকদের কাছে চালিয়েও দিয়েছেন। আমাদের মুক্তির জন্য হেগেলেরও আবশ্যক আছে, শংকরেরও আবশ্যক আছে; কিন্তু তাই বলে হেগেলের মস্তক মুণ্ডন করে তাঁকে আমাদের স্বহস্তরচিত শতগ্রন্থিময় কশ্ব পরিয়ে শংকর বলে সাহিত্যসমাজে পরিচিত করে দেওয়াতে কোনো লাভ নেই। হেগেলকে ফকির না করে যদি শংকরকে গৃহস্থ করতে পারি, তাতে আমাদের উপকার বেশি।
বিজ্ঞান সম্বন্ধেও ঐরূপ ভুল তরজমা অনেক অনর্থ ঘটিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ইভলিউশনের-এর কথাটা ধরা যাক। ইভলিউশনের দোহাই না দিয়ে আমরা আজকাল কথাই কইতে পারি নে। আমরা উন্নতিশীল হই আর স্থিতিশীলই হই, আমাদের সকলপ্রকার শীলই ঐ ইভলিউশন আশ্রয় করে রয়েছে। সুতরাং ইডলিউশনের যদি আমরা ভুল অর্থ বুঝি, তাহলে আমাদের সকল কার্যই যে আরম্ভে পর্যবসিত হবে সে তো ধরা কথা। বাংলায় আমরা ইভলিউশন ‘ক্ৰমবিকাশবাদ’ ‘ক্রমোন্নতিবাদ’ ইত্যাদি শব্দে তরজমা করে থাকি। ঐরূপ তরজমার ফলে আমাদের মনে এই ধারণা জন্মে গেছে যে, মাসিকপত্রের গল্পের মত জগৎ-পদার্থটি ক্রমশ প্রকাশ্য। সৃষ্টির বইখানি আদ্যোপান্ত লেখা হয়ে গেছে, শুধু প্রকৃতির ছাপাখানা থেকে অল্প-অল্প করে বেরচ্ছে, এবং যে অংশটুকু বেরিয়েছে তার থেকেই তার রচনাপ্রণালীর ধরন আমরা জানতে পেরেছি। সে প্রণালী হচ্ছে ক্রমোন্নতি, অর্থাৎ যত দিন যাবে তত সমস্ত জগতের এবং তার অন্তভূত জীবজগতের এবং তার অন্তর্ভুত মানবসমাজের এবং তার অন্তভূত প্রতি মানবের উন্নতি অনিবার্য। প্রকৃতির ধমই হচ্ছে আমাদের উন্নতি সাধন করা। সুতরাং আমাদের তার জন্য নিজের কোনো চেষ্টার আবশ্যক নেই। আমরা শুয়েই থাকি আর ঘুমিয়ে থাকি, জাগতিক নিয়মের বলে আমাদের উন্নতি হবেই। এই কারণেই এই ক্রমোন্নতিবাদ-আকারে ইভলিউশন আমাদের স্বাভাবিক জড়তা এবং নিশ্চেষ্টতার অনকল মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া এই ‘ম’-শব্দটি আমাদের মনের উপর এমনি আধিপত্য স্থাপন করেছে যে, সেটিকে অতিক্রম করা পাপের মধ্যে গণ্য হয়ে পড়েছে। তাই আমরা নানা কাজের উপক্রমণিকা করেই সন্তুষ্ট থাকি, কোনো বিষয়েরই উপসংহার করাটা কর্তব্যের মধ্যে গণ্য করি নে; প্রস্তাবনাতেই আমাদের জীবন-নাটকের অভিনয় শেষ হয়ে যায়। কিন্তু আসলে ইভলিউশন ক্ৰমবিকাশও নয় ক্রমোন্নতিও নয়। কোনো পদার্থকে প্রকাশ করবার শক্তি জড়প্রকৃতির নেই, এবং তার প্রধান কাজই হচ্ছে সকল উন্নতির পথে বাধা দেওয়া। ইভলিউশন জড়জগতের নিয়ম নয়, জীবজগতের ধর্ম। ইভলিউশনের মধ্যে শুধু ইচ্ছাশক্তিরই বিকাশ পরিস্ফট। ইভলিউশন-অর্থে দৈব নয়, পুরুষকার। তাই ইভলিউশনের জ্ঞান মানুষকে অলস হতে শিক্ষা দেয় না, সচেষ্ট হতে শিক্ষা দেয়। আমরা ভূল তরজমা করে ইভলিউশনকে আমাদের চরিত্রহীনতার সহায় করে এনেছি।
ইউরোপীয় সভ্যতার হয় আমরা তরজমা করতে কৃতকার্য হচ্ছি নে, নয় ভুল তরজমা করছি, তাই আমাদের সামাজিক জীবনে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না, বরং অপচয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। অথচ আমাদের বিশ্বাস যে আমরা দু পাতা ইংরেজি পড়ে নব্যব্রাহণসম্প্রদায় হয়ে উঠেছি। তাই আমরা নিজেদের শিক্ষার দৌড় কত সেবিষয়ে লক্ষ্য না করে জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছি। এ সত্য আমরা ভুলে যাই যে, ইউরোপীয় সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান থেকে যদি আমরা নতুন প্রাণ লাভ করে থাকতুম তাহলে জনসাধারণের মধ্যে আমরা নবপ্রাণের সঞ্চারও করতে পারতুম। আমরা অধ্যয়ন করে যা লাভ করেছি তা অধ্যাপনার দ্বারা দেশসুদ্ধ লোককে দিতে পারতুম। আমরা আমাদের cultureকে nationalise করতে পারি নি বলেই গবর্নমেন্টকে পরামর্শ দিচ্ছি যে আইনের দ্বারা বাধ্য করে জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া হোক। মান্যবর শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে মে হজগটির মুখপাত্র হয়েছেন, তার মূলে ইউরোপের নকল ছাড়া আর কোনো মনোভাব নেই। তাই গবর্নমেন্টকে ভজাবার জন্য দিবারাত্রি খালি বিলেতি নজিরই দেখানো হচ্ছে। শিক্ষা-শব্দের অর্থ শুধু লিখতে ও পড়তে শেখা হয়ে দাঁড়িয়েছে। গবর্নমেন্টই স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করে আমাদের লিখতে পড়তে শিখিয়েছেন। সুতরাং গবর্নমেন্টকে গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপন করে রাজ্যিসদ্ধ ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতেই হবে, এই হচ্ছে আমাদের হাল রাজনৈতিক আবদার। যতদিন পর্যন্ত আমরা আমাদের নব-শিক্ষা মজ্জাগত করতে না পারব ততদিন জনসাধারণকে পড়তে শিখিয়ে তাদের যে কি বিশেষ উপকার করা হবে তা ঠিক বোঝা যায় না। আমরা আজ পর্যন্ত ছোটছেলেদের উপযুক্ত একখানিও পাঠ্য পুস্তক রচনা করতে পারি নি। পড়তে শিখলে এবং পড়বার অবসর থাকলে এবং বই কেনবার সংগতি থাকলে প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত চাষার ছেলেরা সেই রামায়ণ-মহাভারতই পড়বেআমাদের নব-শিক্ষার ভাগ তারা কিছু পাবে না। রামায়ণ-মহাভারতের কথা যে বইয়ে পড়ার চাইতে মুখে শোনা অনেক বেশি শিক্ষাপ্রদ, তা নব্যশিক্ষিত ভারতবাসী ছাড়া আর কেউ অস্বীকার করবেন না। মুখের বাক্যে প্রাণ আছে, লেখার ধনিহীন বাক্য আধমরা। সে যাই হোক, আমাদের দেশের লৌকিক শিক্ষার জ্ঞান যদি আমাদের থাকত এবং সেই শিক্ষার প্রতি অযথা অবজ্ঞা যদি আমাদের মনে না স্থান পেত, তাহলে না-ভেবেচিন্তে, লোকশিক্ষার দোহাই দিয়ে, সেই চিরাগত লৌকিক শিক্ষা নষ্ট করতে আমরা উদ্যত হতুম না। সংস্কৃতসাহিত্যের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে তিনিই জানেন যে, আমাদের পূর্বপুরুষরা লোকাচার, লৌকিক ধর্ম, লৌকিক ন্যায় এবং লৌকিক বিদ্যাকে কিরপ মান্য করতেন। কেবলমাত্র বর্ণপরিচয় হলেই লোকে শিক্ষিত হয় না; কিন্তু ঐ পরিচয় লাভ করতে গিয়ে যে বণধর্ম হারানো অসম্ভব নয়, তা সকলেই জানেন। মাসিক পাঁচটাকা বেতনের গুর-নামক গোরর দ্বারা তাড়িত হওয়া অপেক্ষা চাষার ছেলের পক্ষে গোর-তাড়ানো শ্রেয়। ‘ক’-অক্ষর যেকোনো লোকের পক্ষেই গোমাংস হওয়া উচিত নয়, একথা আমরা সকলেই মানি। কিন্তু ‘ক’-অক্ষর যে আমাদের রক্তমাংস হওয়া উচিত, এ ধারণা সকলের নেই। কেবল স্বাক্ষর করতে শেখার চাইতে নিরক্ষর থাকাও ভালো, কারণ পৃথিবীতে আঙুলের ছাপ রেখে যাওয়াতেই মানবজীবনের সার্থকতা। আমাদের আহার পরিচ্ছদ গৃহ মন্দির–সব জিনিসেই আমাদের নিরক্ষর লোকদের আঙুলের ছাপ রয়েছে। শুধু আমবা শিক্ষিতসম্প্রদায়ই ভারতমাতাকে পরিষ্কার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে যাচ্ছি। পতিতের উদ্ধারকার্যটি খুব ভালো; ওর একমাত্র দোষ এই যে, যাঁরা পরকে উদ্ধার করবার জন্য ব্যস্ত তাঁরা নিজেদের উদ্ধার সম্বন্ধে সম্পর্কে উদাসীন। আমরা যতদিন শুধু ইংরেজির নীচে স্বাক্ষর দিয়েই ক্ষান্ত থাকব, কিন্তু সাহিত্যে আমাদের আঙুলের ছাপ ফুটবে না, ততদিন আমরা নিজেরাই যথার্থ শিক্ষিত হব না, পরকে শিক্ষা দেওয়া তো দুরের কথা। আমি জানি যে, আমাদের জাতিকে খাড়া করবার জন্য অসংখ্য সংস্কারের দরকার আছে। কিন্তু আর যে-কোনো সংস্করণের আবশ্যক থাক না কেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাজার হাজার বটতলার সংস্করণের আবশ্যক নেই।
মাঘ ১৩১৯
নারীর পত্র
বীরবলের মারফত প্রাপ্ত
বাঙালি স্ত্রীলোকের পক্ষে ইউরোপের যুদ্ধের বিষয় মতামত প্রকাশ করা যে নিতান্ত হাস্যকর জিনিস তা আমি বিলক্ষণ জানি, অথচ আমি যে সেই কাজ করতে উদ্যত হয়েছি তার কারণ, যখন অনেক গণ্যমান্য লোক এই যুদ্ধউপলক্ষ্যে কথায় ও কাজে নিজেদের উপহাসাপদ করতে কুণ্ঠিত হচ্ছেন না, তখন নগণ্য আমরাই বা পিছপা হব কেন।
একথা শুনে হয়ত তোমরা বলবে, পুরুষের পক্ষে যা করা স্বাভাবিক মেয়ের পক্ষে তা নয়, অতএব পুরুষের অনুকরণ করা স্ত্রীলোকের পক্ষে অনধিকারচর্চা। পরষালি-মেয়ে যে একটি অদ্ভুত জীব একথা আমরা মানি, কিন্তু মেয়েলি-পুরুষ যে তার চাইতেও বেশি অদ্ভুত জীব একথা যে তোমরা মাননা না তার প্রমাণ তোমাদের কথায় ও কাজে নিত্য পাওয়া যায়।
সে যাই হোক, যুদ্ধসম্বন্ধে যে এদেশে স্ত্রীপুরুষের কোনো অধিকারভেদ নেই সে তো প্রত্যক্ষ সত্য। যুদ্ধ তোমরাও কর না, আমরাও করি নে; পল্টন তোমরাও দেখেছ, আমরাও দেখেছি; কিন্তু যুদ্ধ তোমরাও দেখ নি, আমরাও দেখি নি। এবিষয়ে যা-কিছু জ্ঞান তোমরাও যেখান থেকে সংগ্রহ করেছ, আমরাও সেইখান থেকেই করেছি— অর্থাৎ ইতিহাস-নামক কেতাব থেকে। তবে আমাদের ইতিহাস হচ্ছে রামায়ণ-মহাভারত, আর তোমাদের ইংরেজি ও ফরাসি। ভাষা আলাদা হলেও দুইই শোনা কথা এবং সমান বিশ্বাস্য। লড়াই অবশ্য তোমরা কর, কিন্তু সে ঘরের ভিতর ও আমাদের সঙ্গে, এবং তাতেও জিৎ বরাবর যে তোমাদেরই হয় তা নয়। বরং সত্যকথা বলতে হলে, বাল্যবিবাহের দৌলতে বালিকাবিদ্যালয়ের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাথা হেট করেই থাকতে হয়। সুতরাং ইউরোপের এই চতুরঙ্গ-খেলা সম্বন্ধে তোমরা যদি উপর-চাল দিতে পার, তবে আমরা যে কেন পারব না তা বোঝা শক্ত।
কিন্তু ভয় নেই, আমি এ পত্রে কোনোরূপ অধিকারবহির্ভূত কাজ করতে যাচ্ছি নে অর্থাৎ তোমাদের মত কোনো উপর-চাল দেব না; কেননা, কেউ তা নেবে না।
আমাদের মতের যে কোনো মূল্য নেই তা আমরা অস্বীকার করি নে; অপরপক্ষে আমাদের অমত যে মহামূল্য, তাও তোমরা অস্বীকার করতে পার। আমরা তোমাদের মতে চলি, তোমরা আমাদের অমতে চল না। আমাদের ‘না’র কাছে তোমাদের ‘হাঁ’ নিত্য বাধা পায়। আসল কথা, এই অমতের বলে আমরা তোমাদের চালমাৎ করে রেখেছি।
এক্ষেত্রেও তাই আমি এই যুদ্ধ সম্বন্ধে আমার মত নয়, অমত প্রকাশ করতে সাহসী হচ্ছি; কেননা, ‘যুদ্ধ কর’–একথা যদি পুরুষ জোর করে বলতে পারে, তাহলে ‘যুদ্ধ কোরো না’— একথা জোর করে বলতে স্ত্রীলোকে কেন না পারবে? আমরা কাপুরুষ না হলেও না-পুরুষ তো বটেই।
যুদ্ধ যে কস্মিনকালে কোনো দেশে স্ত্রীলোকের অভিপ্রেত হতে পারে না, এবিষয়ে বেশি কথা বলা বৃথা। যুদ্ধ-জিনিসটি চোখে না দেখলেও ব্যাপারখানা যে কি, তা অনুমান করা কঠিন নয়। বঙ্গভাষার মহাকাব্যে যুদ্ধের যে বর্ণনা পড়া যায় আসল ঘটনা অবশ্য তার অনুরূপ নয়। ইউরোপে লক্ষ লক্ষ লোক মিলে আজ যে খেলা খেলছে সে আর যাই হোক ছেলেখেলা নয়। সূর্যগ্রহণ ভূমিকম্প-ঝড়জল-অগ্ন্যুৎপাতের একত্র-আবির্ভাবে পৃথিবীর যেরকম অবস্থা হয়, এই যুদ্ধে ইউরোপের তদ্রপ অবস্থা হয়েছে। এই মহাপ্রলয়গ্রস্ত কোটিকোটি নরনারীর মৃত্যুযন্ত্রণার ও প্রাণভয়ের আর্তনাদ আমাদের কানে অতি শীঘ্র ও অতি সহজে পৌঁছয়; সম্ভবত তা তোমাদের শ্রুতিগোচরই হয় না। অপর কোনো কারণ না থাকলেও এই এক কারণে মানুষের হাতে-গড়া এই মহামারীব্যাপার আমাদের কাছে চিরকালের জন্য হেয় হয়ে থাকত। মায়ের-জাত এমন করে নোক-কাঁদাবার কখনোই পক্ষপাতী হতে পারে না। আমরা নবজীবনের সৃষ্টি করি, সুতরাং সেই জীবন রক্ষা করাই আমাদের মতে মানবের সর্বপ্রধান ধর্ম এবং তার ধংস করা মহাপাপ। তারপর, এই মহাপাপের সৃষ্টি করে পুরুষ, আর তার পরো শাস্তি ভোগ করি আমরা। অতএব যুদ্ধ-ব্যাপারটি আমাদের কি প্রকৃতি, কি স্বার্থ, উভয়েরই সম্পূর্ণ বিরোধী।
তোমরা হয়ত বলবে যে, যুদ্ধের প্রতি শ্রীজাতির এই সহজ বিদ্বেষের মূলে কোনোরূপ যুক্তিসংগত কারণ নেই। সেই কারণে পুরুষে যুদ্ধ সম্বন্ধে শ্রীলোকের মতামত সম্পর্ণে উপেক্ষা করতে বাধ্য। পৃথিবীর বড় বড় জিনিসের ঔচিত্যানচিত্য কেবলমাত্র হদয় দিয়ে যাচাই করে নেওয়া যায় না। এসব ঘটনার সার্থকতা বোঝবার জন্য বিদ্যা চাই, বুদ্ধি চাই।
বিদ্যা যে আমাদের নেই, সে তো তোমাদের গুণে; কিন্তু সেইজন্যে বুদ্ধি যে আমাদের মোটেই নেই একথা আমরা স্বীকার করতে পারি নে। কারণ, ও ধারণাটি তোমাদের প্রিয় হলেও সত্য নয়। সুতরাং যুদ্ধ করা সংগত কি অসংগত— তা আমরা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির সাহায্যে বিচার করতে বাধ্য।
যুদ্ধের সকল সাজসজ্জা সকল রংচং ছাড়িয়ে দেখলে দেখা যায় যে, ওব্যাপারটি হত্যা ও আত্মহত্যা ব্যতীত আর-কিছুই নয়। অথচ এটি প্রত্যক্ষ সত্য যে, মানবজীবনের উদ্দেশ্য যাই হোক, পরকে মারা কিংবা নিজে মরা সে উদ্দেশ্য নয়।
মানুষ পশু হলেও যে হিংস্রপশু নয়, তার প্রমাণ তার দেহ। আমরা হাতে পায়ে মুখে মাথায় অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করে ভূমিষ্ঠ হই নে, তোমরাও হও না। মানুষের অবশ্য নখদন্ত আছে, কিন্তু সে নখ ভালকের নয় এবং সে দাঁত সাপের নয়। অনেকের অবশ্য মস্তকে গোজাতির মগজ আছে এবং অনেকের দেহে গণ্ডারের চর্ম আছে, কিন্তু তাই বলে এ অনুমান করা অসংগত হবে যে, আমাদের পূর্বপুরুষদের ললাটে শঙ্গ এবং নাসিকায় খড়া ছিল। শুনতে পাই যে, আদিম মানবের বহৎ লাগল ছিল, বর্তমানে ও অঙ্গটি অনাবশ্যক। বিধায় সেটি আমাদের দেহচ্যুত হয়েছে। কিন্তু যুদ্ধ করাই যদি যথার্থ মানবধর্ম হয় তাহলে পুরুষ-মানুষের, অন্তত বীর-পুরুষের, মাথার শিং এবং নাকের খাঁড়া খসে পড়বার কোনো কারণ ছিল না। মানুষের কেবল একটিমাত্র ভগবত্ত মহাস্ত্রআছে সেটি হচ্ছে রসনা। সুতরাং মানুষের যুদ্ধপ্রবত্তি ঐ অস্ত্রের সাহায্যেই করা তার পক্ষে স্বাভাবিক এবং কর্তব্য।
তারপর, মানুষ যে আত্মহত্যা করবার জন্য এ পৃথিবীতে আসে নি, তার প্রমাণ মানুষের সকল কাজ, সকল যত্ন, সকল পরিশ্রমের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনধারণ করা। ওই এক মূল-প্রবৃত্তি হতে মানুষের শুধু সকল কর্মের নয়, সকল ধর্মেরও উৎপত্তি। ইহজীবনের পরিমিত সীমা অতিক্রম করবার অদম্য প্রবৃত্তি থেকেই মানুষে দেহাতিরিক্ত আত্মা এবং ইহলোকাতিরিক্ত পরলোকের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছে। এই কারণে, যে কর্মের দ্বারা জীবনরক্ষা সিদ্ধ হয় তাই মানবের নিকট যথার্থ কর্তব্যকর্ম এবং যে ধর্মের চর্চায় আত্মার অমরত্ব সিদ্ধ হয় তাই মানবের নিকট গ্রাহ্যধর্ম। তোমাদের মস্তিপ্রসত দর্শনবিজ্ঞান হাজার প্রমাণাভাব দেখালেও মানুষের মন থেকে যে ধর্মবিশ্বাস দর হয় না তার কারণ মস্তিষ্ক মজ্জার বিকারমাত্র, মজ্জা মস্তিষ্কের বিকার নয়। এবং বাঁচবার ইচ্ছা মানুষের মজ্জাগত। মানুষের কাছে সব জিনিসের চাইতে প্রাণের মূল্য অধিক বলেই প্রাণবধ-করাটাই মানবসমাজে সবচাইতে বড় পাপ বলে গণ্য।
এই কারণেই ‘অহিংসা পরম ধর্ম’— এই বাক্যটিই ধর্মের প্রথম না হক, শেষ কথা। এইকথাটি সত্য বলে গ্রাহ্য করে নিলে যুদ্ধের স্বপক্ষে বলবার আর-কোনো কথাই থাকে না। একের পক্ষে অপরকে বধ করা যদি পাপ হয় তাহলে অনেকে মিলে অনেককে বধ করা যে কি করে ধর্ম হতে পারে তা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। যে গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে অসংখ্য অকর্তব্যকে যোগ দিয়ে একটি মহৎ কর্তব্যে পরিণত করা হয় সে শাস্ত্র আমাদের জানা নেই।
যুদ্ধের মূল যে হিংসা এবং বীরত্ব যে হিংস্রতার নামান্তরমাত্র, সেবিষয়ে অন্ধ থাকা কঠিন।
বীরপুরুষ-নামক জীবের সঙ্গে অবশ্য আমাদের সাক্ষাৎ-পরিচয় নেই। যাত্রাদলের ভীম আর থিয়েটারের প্রতাপাদিত্য হচ্ছে আমাদের বীরত্বের আদর্শ। কিন্তু রঙ্গভূমির বীরত্ব এবং রণভূমির বীরত্বের মধ্যে নিশ্চয়ই অনেকটা প্রভেদ আছে। কেননা, অভিনয়ের উদ্দেশ্য হচ্ছে লোককে আমোদ দেওয়া আর যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে লোককে পীড়ন করা। সুতরাং আসল বীররস যে-পরিমাণে করণ-রসাত্মক নকল বীররস সেই-পরিমাণে হাস্য-রসাত্মক। এর এক থেকে অবশ্য অপরের পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে যেসকল গুণের সমবায়ে বীরচরিত্র গঠিত হয় তার একটি বাদ আর সব গুণই আমাদের শরীরে আছে বলে বীরত্বের বিচার করবার পক্ষে আমরা বিশেষপে যোগ্য।
শুনতে পাই, ধৈর্য হচ্ছে বীর্যের একটি প্রধান অঙ্গ। এ গুণে তোমাদের অপেক্ষা আমরা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। ব্রত নিয়ম উপবাস জাগরণে আমরা নিত্যঅভ্যস্ত, সুতরাং কষ্টসহিষ্ণতা আমাদের অঙ্গের ভূষণ। বিনা-বিচারে বিনাওজরে পরের হকুমে চলা নাকি যোদ্ধর একটি প্রধান ধর্ম। এ ধর্ম আমাদের মত কে পালন করতে পারে? আমাদের মত কলের পুতুল জমানির রাজকারখানাতেও তৈরি হয় নি। তার পর, কারণে কিংবা অকারণে অকাতরে প্রাণদেওয়া যদি বীরত্বের পরাকাষ্ঠা হয়, তাহলে আমরা বীরশ্রেষ্ঠ; কারণ তোমাদের পিতামহেরা যখন জরে মরতেন সেইসঙ্গে আমরা পড়ে মরতুম। এসব গুণ সত্ত্বেও যে আমরা বীরজাতি বলে গণ্য হই নি তার কারণ আমরা পরের জন্য মরতে জানি কিন্তু পরকে মারতে জানি নে। যে প্রবৃত্তির অভাববশত শ্রীধর্ম হেয়, আর সম্ভাববশত ক্ষাত্রধর্ম শ্রেয়–সে হচ্ছে হিংসা। বীরপুরুষ কিছুই সাধ করে ত্যাগ করতে চান না; সবই গায়ের জোরে ভোগ করতে চান। শাস্ত্রে বলে, বীরভোগ্যা বসুন্ধরা’। বীরের ধর্ম হচ্ছে, পৃথিবীর সবণ-পল্প চয়ন করা; অবশ্য আমরাও তার অন্তর্ভূত। তাই আমাদের সঙ্গে বীরপুরুষের চিরকাল ভক্ষ্য-ভক্ষক সম্বন্ধ। বীর প্রাণ দান করতে পারেন না, যদি যুদ্ধক্ষেত্রে দৈবাৎ তা হারান তো সে তাঁর কপাল আর তাঁর শত্রর হাতযশ। বীরত্বের মান্য আজও যে পৃথিবীতে আছে তার কারণ বীরত্ব মানুষের মনে ভয়ের উদ্রেক করে, শ্রদ্ধার নয়। সুতরাং যুদ্ধের মাহাত্ম মানুষের বল নয় দুর্বলতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। যে কাজ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয়, মানুষের ভীরুতাই যার মূলভিত্তি, যে কর্মের ফলে সমাজের অশেষ ক্ষতি হয় তা যে কি করে ধর্ম হতে পারে তা আমাদের ধর্মজ্ঞানে আসে না।
পুরাকালে পুরুষ-মানুষে যুদ্ধ-করাটাই ধর্ম মনে করতেন এবং শ্রীলোকে চিরকালই তা অধর্ম মনে করত। কালক্রমে পুরুষের মনেও এবিষয়ে ধর্মাধর্মের জ্ঞান জন্মেছে। এখন যুদ্ধ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, এক ধর্মযুদ্ধ আর-এক অধর্মযুদ্ধ। শুনতে পাই, এ কার্যের ধর্মাধর্ম তার কারণের উপর নির্ভর করে। সভ্যজাতির মতে আত্মরক্ষার জন্য যে যুদ্ধ, একমাত্র তাই ধর্মবাদবাকি সকল কারণেই তা অধর্ম। এ মতের প্রতিবাদ করা অসম্ভব হলেও পরীক্ষা করা আবশ্যক। কেননা, কথাটা শুনতে যত সহজ আসলে তত নয়। এই দেখ না, ইউরোপে কোনো জাতিই এই যুদ্ধের দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে নিতে চান না এবং পরস্পর পরস্পরকে অধর্মযুদ্ধ করবার দোষে দোষী করছেন; অথচ এরা সকলেই সভ্য, সকলেই বিদ্বান ও সকলেই বুদ্ধিমান। এই মতভেদের কারণ কি এই নয় যে, আত্মরক্ষা-শব্দের অর্থটি তেমন সুনির্দিষ্ট নয়। আত্ম’শব্দের অর্থ কে কি বোঝেন, আত্মজ্ঞানের পরিসরটি কার কত বিস্তৃত তার দ্বারাই তাঁর আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধক্ষেত্রের প্রসারও নির্নীত হয়। পরদ্রব্যে যে মানুষের আত্মজ্ঞান জন্মাতে পারে তার প্রমাণ পৃথিবীতে বহু ব্যক্তি এবং বহু জাতি নিত্যই দিয়ে থাকেন। সুতরাং কোন পক্ষ যে শুদ্ধ আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করছেন আর কোন পক্ষ যে শুধু পরদ্রোহিতার জন্য যুদ্ধ করছেন, নিরপেক্ষ দর্শকের পক্ষে তা বলা কঠিন।
আত্মরক্ষা-শব্দের অবশ্য একটা জানা অর্থ আছে; সে হচ্ছে আক্রমণকারীর হাত থেকে নিজের প্রাণ ও নিজের ধন রক্ষা করা; এবং সে ধনও বর্তমান ধন, ভূত কিংবা ভবিষ্যৎ নয়। কেননা, গত ধন পুনরুদ্ধার কিংবা অনাগত ধন আত্মসাৎ করবার জন্য পরকে আক্রমণ করা দরকার।
পৃথিবীর সকল জাতিই যদি উক্ত সহজ ও সংকীর্ণ অর্থে আত্মরক্ষা ব্যতীত অপর-কোনো কারণে যুদ্ধ করতে গররাজি হন, তাহলে যুদ্ধ কালই বন্ধ হয়ে যাবে। কারণ, কেউ যদি আক্ৰমণ না করে তো আর-ক’কেও আত্মরক্ষা করতে হবে না। যুদ্ধ থেকে নিরস্ত হওয়াই যদি পুরুষজাতির মনোগত অভিপ্রায় হয়, তাহলে নিরস্ত্র হওয়াই তার অতি সহজ উপায়। সুতরাং যতদিন দামামা-কাড়া ঢাল-তলোয়ার গুলি-গোলা ইত্যাদি সভ্যতার সর্বপ্রধান অঙ্গ হয়ে থাকবে, ততদিন আত্মরক্ষা করা যে যুদ্ধের একমাত্র কিংবা প্রধান কর্তব্য একথা বলা চলবে, কিন্তু মানা চলবে না।
আসল কথা, যুদ্ধের দ্বারা আত্মরক্ষা করা দুর্বল জাতির পক্ষে অসম্ভব এবং প্রবল জাতির পক্ষে অনাবশ্যক।
দুর্বলের পক্ষে ও-উপায়ে আত্মরক্ষা করবার চেষ্টা করার অর্থ আত্মহত্যা করা। হাতে-হাতে প্রমাণ বেলজিঅম।
যুদ্ধ আমাদের মতে একমাত্র সেই-ক্ষেত্রে ধর্ম যে-ক্ষেত্রে প্রবলের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-স্বরূপে, দুর্বল এই উপায়ে আত্মরক্ষা নয়, আত্মবিসর্জন করে। উদাহরণ–বেলজিঅম।
সত্যকথা বলতে গেলে মানুষে হয় অর্থের জন্য নয় প্রভুত্বের জন্য, হয় রাজ্যের জন্য নয় গৌরবের জন্য পরের ঘাড়ে গিয়ে পড়ে। পরার্থনাশ এবং স্বার্থসাধনের জন্যই যুদ্ধ আরম্ভ করা হয়। যুদ্ধের মূলে আত্মজ্ঞান নেই, আছে শুধু অহংজ্ঞান। যুদ্ধের উৎপত্তি থেকেই তার চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।
যুদ্ধে যে ধর্মকার্য এ প্রমাণ করতে হলে তৎপূর্বে ‘হিংসা পরম ধর্ম” এই সত্যের প্রতিষ্ঠা করা দরকার। তোমরা অবশ্য এ কর্তব্যকার্যে পরাঙ্খ হও নি। বুদ্ধের ধর্ম যে বুদ্ধির ধর্ম নয় এই প্রমাণ করবার জন্য, শুনতে পাই, বুদ্ধিমান পুরুষ নানা দর্শন ও বিজ্ঞান রচনা করেছেন।
বাংলার মাসিকপত্রের প্রসাদে এসম্বন্ধে পণ্ডিতমণ্ডলীর বিধানগুলির কিঞ্চিৎ পরিচয় আমরাও লাভ করেছি। দেশের ও বিদেশের এইসকল ব্রাহরণপণ্ডিতদের, মাথার না হোক, বুকের মাপ আমরা নিতে জানি। বড়-বড় কথার আড়ালেও তোমাদের হদয়বিকার আমাদের কাছে ধরা পড়ে। তাই তোমাদের দর্শনবিজ্ঞানে তোমাদের ঠকাতে পারে, আমাদের পারে না।
শুনতে পাই, অক্লান্ত গবেষণার ফলে বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করেছেন যে, মানুষ পচ্ছবিষাণহীন হলেও পশ। এবং যেহেতু পশর জীবন সংগ্রামসাপেক্ষ অতএব দুর্বলের উপর আক্রমণ এবং প্রবলের নিকট হতে পলায়ন করাই মানুষের স্বধর্ম। ছল ও বল প্রয়োগের দ্বারাই মানুষ তার অন্তর্নিহিত মানসিক ও শারীরিক শক্তির পণ পরিণতি লাভ করতে পারে। সুতরাং পশুত্বের চর্চা করাই হচ্ছে যথার্থ মনুষ্যত্বের চর্চা করা। যে-সভ্যতা নিষ্ঠুরতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, সে-সভ্যতা শক্তিহীন ও প্রাণহীন; কেননা, হিংসাই হচ্ছে জীবজগতের মূলসত্য। এবং সেই সত্যের উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত করাই হচ্ছে ধর্ম। হিংসা ও প্রতিহিংসার ঘাতপ্রতিঘাতই মানবের উন্নতির একমাত্র কারণ; এবং নিজের নিজের উন্নতি সাধন করাই যে পরম পুরষার্থ–সেবিষয়ে আর সন্দেহ নেই। আমরা অজ্ঞযুগের উত্তরাধিকারীশতে যেসকল নীতিজ্ঞান লাভ করেছি তার চর্চায় মানুষকে শুধু দুর্বল করে। সুতরাং নবনীতির বিধান এই যে, নির্মমভাবে যুদ্ধ কর, অবশ্য দুর্বলের সঙ্গে।
এতটা নগ্ন সত্য মানুষে সহজে বুকে তুলে নিতে পারে না; কেননা, তা তার যুগসতি সংস্কারের বিরুদ্ধে যায়। সাধারণ লোকের সে পরিমাণ বুদ্ধিবল নেই, যাতে করে জীবজগতে অবরোহণ করাই যে আরোহণ করবার একমাত্র উপায়— এ সত্য সহজে আয়ত্ত করতে পারে। তাছাড়া, সকলের সে পরিমাণ তীক্ষ অন্তদটি নেই যার সাহায্যে নিজের বুকের ভিতর হিংস্র পশুর সাক্ষাৎকার লাভ করতে পারে।
সুতরাং এই বৈজ্ঞানিক সত্যটিকে সাধারণের নিকট গ্রাহ্য করাতে হলে তাকে ধর্ম ও নীতির সাজে সজ্জিত করে বার করা দরকার। অতঃপর বৈজ্ঞানিকরা সেই উপায়ই অবলম্বন করেছেন।
সুনীতির ছদ্মবেশধারী বৈজ্ঞানিক মত এই। প্রতি লোক নিরীহ হলেও তাদের সমষ্টিতে সমাজ-নামক যে বিরাটপুরুষের সৃষ্টি হয়, সে একটি ভীষণ জীব। এই বিরাটপুরুষের প্রাণ আছে আত্মা নেই, রতি আছে বুদ্ধি নেই, গতি আছে দৃষ্টি নেই। সমাজ শুধু বাঁচতে চায় ও বাড়তে চায়, এই তার জীবনের ধর্ম; অন্যকোনো ধর্মাধর্ম তাকে স্পর্শ করে না। সমাজ হচ্ছে একমাত্র অঙ্গী এবং ব্যক্তিমাত্রেই তার অঙ্গ। সুতরাং ব্যক্তিমাত্রেই সমাজের অধীন কিন্তু সমাজ কোনো ব্যক্তিবিশেষের অধীন নয়। এবং যেহেতু সমাজের বাইরে আমাদের কোনো অস্তিত্ব নেই, সে কারণ সমাজকে রক্ষা করা এবং তার অভ্যুদয়সাধন করাই হচ্ছে মানুষের পক্ষে সর্ব প্রধান কর্তব্য। সহস্র সহস্র লোকের আত্মবলিদানের ফলে এই বিরাটপুরুষের দেহ পুষ্ট হয়। লোকে বলে যে, যে মণ্ডপের আঙিনায় লক্ষ বলি হয়, সেখানে একটি কবন্ধ-ভূত জন্মায়, যার নরবলি ব্যতীত আর-কোনো উপায়ে ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করা যায় না; এবং সে বভুক্ষিত থাকলে গহস্থের ঘাড় মটকে খায়। বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত সমাজনামক বিরাটপুরুষ এই জাতীয় একটি প্রেতযোনি বই আর-কিছুই নয়। এই বিরাট-কবন্ধের শোণিত-পিপাসা নিবারণাৰ্থ নরবলি দেওয়া ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের অবশ্য কর্তব্য। বলা বাহুল্য, পৃথিবীতে যতগুলি বিভিন্ন সমাজ আছে, ততগুলি পথক টিপুরুষও আছে। এবং এইসকল নরমাংস-লোলপ দৈত্যদের মধ্যে চিরশত্রতা বিদ্যমান। সুতরাং মানুষের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য নিজ-সমাজের নিকট পর-সমাজকে বলি দেওয়া, অর্থাৎ যুদ্ধ করা। এই মতাবলম্বী বৈজ্ঞানিকরা মানবের নৈতিক বুদ্ধির অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, শুধু তার বিকার সাধন করে সেটিকে বিপথে চালাতে চান। এদের শাদা কথা এই যে, নিজের স্বার্থের জন্য করলে যে কাজ মহাপাপ, জাতীয় স্বার্থের জন্য করলে সেই একই কাজ মহাপণ্য। সমাজ-নামক অপদেবতাকে নিবেদন করে দিলে খুন জখম চুরি ডাকাতি ফলের মত শুভ্র দীপের ন্যায় উজ্জ্বল ধপের ন্যায় সুরভি হয়ে ওঠে। বহু মানবকে একত্রে যোগ দিলে কি করে একটি দানবের সৃষ্টি হয় তা আমাদের শ্রীবৃদ্ধির অতীত। আর এইকথাটা জিজ্ঞাস্য থেকে যায় যে, লোকসমষ্টিকে সমাজ নাম দিয়ে তার উপরে ব্যক্তিত্ব আরোপ করার যদি কোনো বৈধ কারণ থাকে তাহলে এই ব্যক্তিটির অন্তরে একটি আত্মার আরোপ করা কি কারণে অবৈধ? এই বিরাটপুরুষকে মানবমী কল্পনা করলে আমাদের সহজ ন্যায়বৃদ্ধিকে ডিগবাজি-খাওয়াবার জন্য তোমাদের আর এত গলদঘর্ম হতে হত না।
বিজ্ঞান মানুষকে মারতে শেখালেও মরতে শেখাতে পারে না। এইজন্যই দর্শনের আবশ্যক। মানুষে সহজে দেহ-পিঞ্জর থেকে আত্মা-পাখিটিকে মুক্তি দিতে চায় না; কেননা, ভবিষ্যতে তার গতি কি হবে সেবিষয়ে সকলেই অজ্ঞ। আত্মার সঙ্গে বর্তমানে আমাদের সকলেরই পরিচয় আছে এবং তার ভবিষ্যৎঅস্তিত্বের আশা আমরা সকলেই পোষণ করি। এর বেশি আমরা আর-কিছুই জানি নে। অপরপক্ষে, দার্শনিকেরা আত্মার ভূত-ভবিষ্যতের সকল খবরই জানেন। সুতরাং অমরত্বের আশাকে বিশ্বাসে পরিণত করবার ভার তাঁদের হাতে। এবং তাঁরাও তাঁদের কর্তব্যপালন করতে কখনও পশ্চাৎপদ হন নি। যুদ্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য অবশ্য মারা, মরা নয়; তবে হত্যা করতে গেলে হত হবার সম্ভাবনা আছে বলে দার্শনিকেরা এই সত্য আবিষ্কার করেছেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে দেহত্যাগ করলে আত্মা একলক্ষে স্বর্গারোহণ করে এবং সেদেশে উপস্থিত হওয়ামাত্র এত ভোগবিলাসের অধিকারী হয় যে, তা এ পৃথিবীর রাজরাজেশ্বরেরও কল্পনার অতীত। কিন্তু অর্ধব ইন্দ্রের ইন্দ্ৰত্বের লোভে ধ্রুব ত্যাগ করা সকলের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। সকাল-সকাল স্বর্গপ্রাপ্তির সম্বন্ধে যোদ্ধাদের তাদশ উৎসাহ না থাকায়, তাদের উৎসাহ-বর্ধনের জন্য সঙ্গেসঙ্গে নরকেরও ভয় দেখানো হয়। কিন্তু তাতেও যদি ফল না হয় তো সেনাপতিরা যুদ্ধ-পরাঙ্খ সৈনিকদের বধ করতে পারেন, এবিষয়েও দার্শনিক বিধি আছে। অর্থাৎ মৃত্যুভয় দেখিয়ে মানুষকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত করতে হয়।
দুর্ভাগ্যবশত অত কাঁচা ওষুধ সকলের ধরে না। পৃথিবীতে এমন লোক দুর্লভ নয়, যাঁরা মানুষকে মারতে প্রস্তুত নন স্বর্গের লোভেও নয়, নরকের ভয়েও নয়। এদের যুদ্ধে প্রবত্ত করাবার উপযোগী দর্শনও আছে। যাঁরা নিজের স্বার্থের জন্য পরের ক্ষতি করতে প্রস্তুত নন, তাঁদের নিঃস্বার্থতার দিক দিয়ে বাগাতে হয়। যিনি মর্তরাজ্য কি স্বর্গরাজ্য কোনো রাজ্যই কামনা করেন না, তাঁকে নিষ্কাম হত্যা করবার উপদেশ দেওয়া হয়। হত্যা পাপ নয়, কারণ ও একটি কর্ম। কম করাই ধর্ম, তার ফল কামনা করাই অধর্ম। হত্যা করা যে পাপ এ ভ্রান্তি শুধু তাদেরই হয় যারা আত্মার ভূত-ভবিষ্যতের বিষয় অজ্ঞ। আত্মা যখন অবিনশ্বর তখন কেউ কাউকে বধ করতে পারে না। দেহ আত্মার বসনমাত্র। সুতরাং প্রাণবধ করার অর্থ আত্মাকে পুরনো কাপড় ছাড়িয়ে নূতন কাপড় পরানো। অপরকে নূতন বস্ত্র দান করা যে পুণ্যকার্য সে তো সর্ববাদিসম্মত। মানুষ যদি তার ক্ষুদ্র হদয়দৌর্বল্য অতিক্রম করে নিজের অমরত্ব অর্থাৎ দেবত্ব অনুভব করে, তাহলে নিষ্ফল হত্যা করতে তার আর কোনো দ্বিধা হবে না। অপরকে বধ করবার সফলটি নিজে ভোগ না করলেও আর-দশজনকে যে তার কুফল ভোগ করতে হয় তা উপেক্ষা করা কর্তব্য। পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি হদয়দৌর্বল্য হতে আত্মজ্ঞানী পুরুষ চিরমুক্ত। অতএব নির্মমভাবে যুদ্ধ কর।
পূর্বোক্ত বৈজ্ঞানিক মত বিদেশের এবং দার্শনিক মত এদেশের। বলা বাহুল্য যে, দুই একই-মতের এ-পিঠ আর ও-পিঠ।
এইসব দর্শনবিজ্ঞানের সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে, যুদ্ধ-করাটা মানবধর্ম নয়। যদি তা হত তো মানবকে হয় দানব, নয় দেবতা, নয় পশ, প্রমাণ করতে দর্শনবিজ্ঞানের সিংহব্যাঘ্রেরা এতটা গর্জন করতেন না।
আসল কথা, বুদ্ধি-ব্যবসায়ীরা মানবসমাজকে মাথার উপর দাঁড় করাতে চান, কাজেই তা উলটে পড়ে।
এসকল দর্শনবিজ্ঞান যে মনের বিকারের লক্ষণ তার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। জরে মাথায় খুন চড়ে গেলে মানুষে যে প্রলাপ বকে তার পরিচয় এই ম্যালেরিয়ার দেশে আমরা নিত্যই পাই। দঃখের বিষয়, এই যুদ্ধ-জর যেমন মারাত্মক তেমনি সংক্রামক। এ হচ্ছে মনের প্লেগ। এ যুগে শরীরের প্লেগ হয় এশিয়ায় আর মনের প্লেগ হয় ইউরোপে— এ দুয়ের ভিতর এই যা প্রভেদ। ইউরোপ বিজ্ঞানের বলে দেশ থেকে প্লেগ তাড়িয়েছে, মন থেকে কি তা তাড়াতে পারবে না?
এ পাপ দূর করতে যে মনের বল, যে চরিত্রের বল চাই, এককথায় যে বীরত্ব চাই–সে বীরত্ব তোমাদের নরসিংহ ও নরশাদলদের দেহে নেই। স্ত্রীলোকের পক্ষে পুরুষ-চরিত্র অনুকরণ করা যে হাস্যকর তার কারণ মানবজাতি যদি যথার্থ সভ্য হতে চায় তো পুরুষের পক্ষে শ্রী-চরিত্রের অনুকরণ করা কত ব্য। তোমাদের দেহের বলের সঙ্গে আমাদের মনের বলের, তোমাদের বন্ধিবলের সঙ্গে আমাদের চরিত্রবলের যদি রাসায়নিক যোগ হয় তাহলেই তোমরা যথার্থ বীরপুরুষ হবে, নচেৎ নয়। কারণ খাঁটি বীরত্বের ধর্ম হচ্ছে পরকে মারা নয়, বাঁচানো; পরের জন্য নিজে মরা নয়, বেত থাকা। মানুষে ক্ষণিক নেশার ঝোঁকে পরের জন্য দেহত্যাগ করতে পারে, কিন্তু পরের জন্য চিরজীবন আত্মােৎসর্গ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রজ্ঞার আবশ্যক। সতরাং যথার্থ নিষ্কাম ধর্ম হচ্ছে শ্রীধর্ম, ক্ষাত্রধর্ম নয়।
এর উত্তরে ঐতিহাসিক বলবেন, আজ তিন হাজার বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর ঢের বদল হয়েছে কিন্তু যুদ্ধ বরাবর সমানই চলে আসছে, সুতরাং তা চিরদিনই থাকবে। এর প্রত্যুত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, পুরুষজাতির ভিতর যদি এমন-একটি আদিম পশুত্ব থাকে যার উচ্ছেদ অসম্ভব, তাহলে তাদের লালনপালন করবার মত তাদের শাসন করবার ভারও আমাদের হাতে আসা উচিত। আমরা শাসনকত্রী হলে পৃথিবীর যুদ্ধক্ষেত্রকে শ্রীক্ষেত্রে পরিণত করব এবং তোমাদের পোষ মানিয়ে জগবন্ধুর রথ টানাব। ইতি
জনৈক বঙ্গনারী
কার্তিক ১৩২১
নারীর পত্রের উত্তর
আমরা স্বীজাতিকে সমাজে স্বাধীনতা দিই নি, কিন্তু সাহিত্যে দিয়েছি। আজকাল বাংলাভাষায় লেখকের চাইতে লেখিকার সংখ্যাই বেশি। সম্ভবত সেই কারণে মাসিকপত্ৰসকল পত্রিকা’সংজ্ঞা ধারণ করেছে। স্ত্রীজাতি এতদিন সে স্বাধীনতার অপব্যবহার করেন নি; কেননা, মতামতে তাঁরা একালযাবৎ আমাদেরই অনুসরণ করে আসছেন। বাংলায় স্ত্রী-সাহিত্য জলমেশানো পং-সাহিত্য বই আর কিছুই নয়, সুতরাং সে সাহিত্য পরিমাণে বেশি হলেও আমাদের সাহিত্যের চাইতেও ওজনে ঢের কম ছিল।
কিন্তু লেখিকারা যদি স্ত্রী-মনোভাব প্রকাশ করতে শুরু করেন, তাহলে তাঁদের কথা আর উপেক্ষা করা চলবে না। এই কারণে, এইসঙ্গে যে নারীর পত্রখানি পাঠাচ্ছি, তার মতামত সম্বন্ধে সসংকোচে দুটি-একটি কথা বলতে চাই।
লেখিকার মূলকথার বিরুদ্ধে বিশেষ-কিছু বলবার নেই। সেকথা হচ্ছে এই যে, যুদ্ধ না-করা প্রজাতির পক্ষে স্বাভাবিক। এই স্বতঃসিদ্ধ সত্য প্রমাণ করবার জন্য অত বাগজাল বিস্তার করবার আবশ্যক ছিল না। অপরপক্ষে, যুদ্ধ করা যে পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক, তা প্রমাণ করাও অনাবশ্যক। এই সত্যটি মেনে নিলে লেখিকা দর্শন-বিজ্ঞানের প্রতি অত আক্রোশ প্রকাশ করতেন না। দর্শন-বিজ্ঞান যুদ্ধের সৃষ্টি করে নি, যুদ্ধই তদনুরূপ দর্শন-বিজ্ঞানের সৃষ্টি করেছে। ক্ষত্রিয়ের অস্ত্র হচ্ছে ব্রাহমণের পণ্ঠপোষক, তাই ব্রাহমণের শাস্য ক্ষত্রিয়ের চিত্ততোষক হতে বাধ্য। এ দুই জাতির ভিতর স্পষ্ট সাংসারিক বাধ্যবাধকতার সম্বন্ধ আছে; কিন্তু যুদ্ধজীবীর সঙ্গে বুদ্ধিজীবীর যে একটি মানসিক বাধ্যবাধকতাও আছে, তা সকলের কাছে তেমন সস্পষ্ট নয়। একদল মানুষে যা করে, আর-এক দলে হয় তার ব্যাখ্যান নয় ব্যাখ্যা করে। কমবীর জ্ঞানহীন হতে পারে, এবং জ্ঞানবীর কর্মহীন হতে পারে; কিন্তু পৃথিবীতে কর্ম না থাকলে জ্ঞানও থাকত না। কর্ম জ্ঞানবৃক্ষের ফল নয়, জ্ঞান কর্মক্ষের ফল। সুতরাং যুদ্ধের দায়িত্ব দর্শনবিজ্ঞানের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে উধোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে চাপাননা। মানুষ যতদিন যুদ্ধ করবে, মানুষে ততদিন হয় তার সমর্থন নয় তার প্রতিবাদ করবে। মানুষকে ঝগড়া-লড়াই করতে উসকে দেওয়াই যে জ্ঞানের একমাত্র কাজ, তা অবশ্য নয়। আনীমাত্রেই যে নারদ নন, তার প্রমাণ স্বয়ং বুদ্ধদেব।
লেখিকা ধর্মযুদ্ধ এবং অধর্মযুদ্ধের পার্থক্য স্বচ্ছন্দচিত্তে মানতে চান। তাঁর মতে এই ‘অভেদ পার্থক্যের আবিষ্কারে পুরুষজাতি বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন, হৃদয়ের নয়। হদয় ও বুদ্ধির পার্থক্যও যে কাল্পনিক, এ সত্যটি মনে রাখলে যা আসলে অবিচ্ছেদ্য তার বিচ্ছেদ ঘটিয়ে তার এক অংশ আমাদের দিয়ে অপর অংশ প্রীজাতি অধিকার করে বসতেন না। বুদ্ধিও আমাদের একচেটে নয়, হদয়ও ওঁদের একচেটে নয়; এবং যেমন হৃদয়ের অভাবের নাম বুদ্ধি নয়, তেমনি বুদ্ধির অভাবের নামও হদয় নয়। সুতরাং একথা নিয়ে বলা যেতে পারে যে, যুদ্ধের ধর্মাধর্মের বিচারে পুরুষজাতি বুদ্ধি ও হদয় দুয়েরই সমান পরিচয় দিয়েছেন। কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা কঠিন হলেও ধর্মক্ষেত্রে যুদ্ধ সম্বন্ধে বিধিনিষেধ মান্য।
‘অহিংসা পরম ধর্ম’–এই বাক্য বৌদ্ধধর্মের মূলকথা হলেও বৌদ্ধশাস্ত্রেই স্বীকৃত হয়েছে যে, মানুষ পেটের দায়ে যুদ্ধ করে। উদরকে মস্তিষ্ক যে পরোপরি নিজের শাসনাধীন করতে পারে না, তার জন্য দায়ী মানুষের প্রকৃতি নয়, তার আকৃতি। দেহ ও মনে, কর্মে ও জ্ঞানে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়–তখন শান্তির জন্য একেও কিছু ছেড়ে দিতে হয়, ওকেও কিছু ছেড়ে দিতে হয়। হিংসা এবং অহিংসার সন্ধি থেকেই বৈধ হিংসার সৃষ্টি হয়। আর, সন্ধ্যা-জিনিসটি–তা সে প্রাতঃই হোক আর সায়ংই হোক— পুরো আলোও নয়, পুরো অন্ধকারও নয়। সুতরাং যুদ্ধ-জিনিসটি একদম শাদাও নয়, একদম কালোও নয়; ওই দুয়ে মিলে যা হয় তাই, অর্থাৎ ছাই।।
লেখিকা আমাদের প্রতি–অর্থাৎ বাঙালি পরিষের প্রতি যে কটাক্ষ করেছেন, সে অবশ্য সে-জাতীয় বদৃষ্টি নয় যার সম্বন্ধে কবিতা লিখে লিখে আমরা এলি নে। এসম্বন্ধে আমি কোনোরূপ উচ্চবাচ্য কবে না; কেননা, লেখিকা স্বীকার করেছেন যে, রসনা হচ্ছে মহাস্ত্র। দুর্বল আমরা অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতে জানি নে; কিন্তু অবলা ওঁরা যে ও-মহাস্ত্র ব্যবহার করতে জানেন সেবিষয়ে কেউ আর সন্দেহ করেন না; কেননা, সকলেই ভুক্তভোগী।
সে যাই হোক, সাধারণ পুরুষজাতি সম্বন্ধে তাঁর মতের প্রতিবাদ করা যেতে পারে। তিনি পুরুষের স্বভাব অতি অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন; কেননা, তা স্বীস্বভাব নয়। মানুষের স্বভাব যে কি, লেখিকা যদি তা জানেন তাহলে তিনি এমনি-একটি জিনিসের সন্ধান পেয়েছেন, যা আমরা যুগযুগান্তের অনুসন্ধানেও পাই নি। আমরা যেমন কোনো অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করে জন্মগ্রহণ করি নি তেমনি কোনো প্রাক্তন সংস্কার নিয়ে জন্মাই নি। আমরা দেহ ও মনের নগ্ন অবস্থাতেই পৃথিবীতে আসি। তাই আমরা মনুষ্যত্বের তত্ত্বের জন্য কখনো পশর কাছে কখনো দেবতার কাছে যাই। কারণ এসব-জাতীয় জীবের একটা বাঁধাবাঁধি বিধিনির্দিষ্ট প্রকৃতি আছে; শুধু আমাদের নেই। আমরা শুধু স্বাধীন, বাদবাকি সৃষ্টি নিয়মের অধীন। সুতরাং আমরা মানবজীবনের যখনই একটি বাঁধাবাঁধি নিয়মের আশ্রয় পতে চাই, তখনই আমাদের মনুষ্যেতর জীবের দ্বারস্থ হতে হয়। নসিংহও আমাদের আদর্শ, নরহরিও আমাদের আদর্শ; শুধু আমরা আমাদের আদর্শ নই। মনুষ্যত্ব প’ড়ে-পাওয়া যায় না, কিন্তু গ’ড়ে-নিতে হয় এই সত্য মানুষে যতদিন না গ্রাহ্য করবে, ততদিন ভিক্ষুকের মত তাকে পরের দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে। যদি বল যে, প্রত্যক্ষ পশু কিংবা অপ্রত্যক্ষ দেবতা মানুষের আদর্শ হতে পারে না, তাহলে মানুষে উদ্ভিদকে তার আদর্শ করে তুলবে। এ কাজ মানুষে পূর্বে করেছে এবং বাধ্য হলে পরেও করবে। মানুষ যদি মানুষ না হতে শেখে, তাহলে উদ্ভিদ হওয়ার চাইতে তার পক্ষে পশু হওয়া ভালো; কেননা, পশু জঙ্গম, আর উদ্ভিদ স্থাবর। মনুষ্যত্বকে স্থাবর করতে হলে মানুষকে জড় মক অন্ধ ও বধির হতে হবে। আর তাছাড়া উদ্ভিদ হলে আমরা ভক্ষক হই, ভক্ষ্য হব।
লেখিকা যদি এখানে প্রশ্ন করেন যে, কোনো-একটা আদর্শ না পেলে কার সাহায্যে মানুষ একটি স্থায়ী মনুষ্যত্ব গড়ে তুলবে: তার উত্তরে আমি বলব, মানুষের মানুষকে নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে। যেমন, আমরা একটা লেখা গড়ে তুলতে হলে, যতক্ষণ আমাদের ক্ষমতার সীমায় পৌঁছই ততক্ষণ ক্রমান্বয়ে কাটি আর লিখি; তেমনি সভ্যতা-পদার্থটিও ততক্ষণ বারবার ভেঙে গড়তে হবে, যতক্ষণ মানুষ তার ক্ষমতার সীমায় না পৌঁছয়। সেদিন যে কবে আসবে কেউ বলতে পারে না, সম্ভবত কখনোই আসবে না। রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি ধর্মনীতি দর্শন বিজ্ঞান যে পরিমাণে এই এক্সপেরিমেন্টের কাজ করে, সে পরিমাণে তা সার্থক; এবং যে পরিমাণে তা নূতন এক্সপেরিমেন্টকে বাধা দেয়, সে পরিমাণে তা অনর্থক। মানুষ সম্বন্ধে শেষকথা এই যে, তার সম্বন্ধে কোনো শেষকথা নেই।
সাধারণত যুদ্ধ-ব্যাপারটি উচিত কি অনুচিত, সে আলোচনার সার্থকতা যাই হোক, কোনো-একটি বিশেষ-যুদ্ধের ফলাফল কি হবে, সে বিচারের মুল্য মানুষের কাছে ঢের বেশি।
এই বর্তমান যুদ্ধই ধর না কেন। পৃথিবীসদ্ধ লোক এই ভেবে উদ্বেজিত উত্তেজিত এবং উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে যে, ইউরোপের হাতে-গড়া সভ্যতা এইবার ইউরোপ বুঝি নিজের হাতে ভাঙে। যদি ইউরোপের সভ্যতা এই ধাক্কায় কাৎ হয়ে পড়ে তো বুঝতে হবে যে, সে সভ্যতার ভিত অতি কাঁচা ছিল। তাই যদি প্রমাণ হয়, তাহলে ইউরোপকে এই ধংসাবশেষ নিয়ে ভবিষ্যতে এর চাইতে পাকা সভ্যতা গড়তে হবে। ঠেকো দিয়ে রাখার চাইতে ঝাঁকিয়ে দেখা ভালো যে, যে-ঘরের নীচে আমরা মাথা রাখি সে-ঘরটি ঘুনে-খাওয়া কি টেকসই। কিন্তু এই ভূমিকম্পে যে ইউরোপের অট্টালিকা একেবারে ধরাশায়ী হবে, সে আশঙ্কা করবার কোনো কারণ নেই। ‘ধূলিসাৎ হবে শুধু তার দপের চড়া, আর তার ঠেকো-দিয়ে-রাখা প্রাচীন অংশ, আর তার গোঁজামিলন-দিয়ে-তৈরি নতুন অংশ। এতে মানবজাতির লাভ বই লোকসান নেই। তাছাড়া, এই যুদ্ধের ফলে ইউরোপের একটি মহা লাভ হবে তার এই চৈতন্য হবে যে, সে এখনো পুরোপুরি সভ্য হয় নি। বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান হয়ে ইউরোপ আত্মজ্ঞান হারাতে বসেছিল; এই যুদ্ধের ফলে সে আবার আত্মপরিচয় লাভ করবে। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। লেখিকা বলেছেন যে, যধরপ মানসিক প্লেগ ইউরোপে আছে, এশিয়ায় নেই। এশিয়ার লোকের যে মনে পাপ নেই সেকথা বলা চলে না; কেননা, লেখিকাই দেখিয়েছেন যে, কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য উভয় শাস্ত্রই যুদ্ধ সম্বন্ধে একই মন্ত্র পুরুষজাতির কানে দিয়েছেন। তবে এশিয়া যে শান্ত আর ইউরোপ যে দদন্তি, তার কারণ মন ছাড়া অন্যত্র খুজতে হবে। প্রাচ্যদর্শন শুধু মন্ত্র দিতে পারে, কিন্তু পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান শুধু মন্ত্র নয়, সেই মন্ত্রের সাধনোপযোগী যন্ত্রও মানুষের হাতে দিয়েছে। বিজ্ঞান মানুষের জন্য শুধু শাস্ত্র নয়, অস্ত্রশস্ত্রও গড়ে দিয়েছে। সে অস্ত্রের সাহায্যে মানুষে পঞ্চভূতকে নিজের বশীভূত করেছে, কিন্তু নিজেকে বশ করতে পারে নি। সুতরাং অনেকে মনে করতেন যে, বিজ্ঞান হয়তো অমানুষের হাতে খন্তা দিয়েছে। যদি এ যুদ্ধে প্রমাণ হয়ে যায় যে ঘটনাও তাই, তাহলে ইউরোপীয়েরা মানুষ হতে চেষ্টা করবে। কারণ ও খন্তা কেউ ত্যাগ করতে পারবে না; শুধু সেটিকে ভবিষ্যতে ভাইয়ের বিরদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার না করে জড়প্রকৃতির শাসনের যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে— অর্থাৎ প্রলয় নয়, সৃষ্টির কাজে তা নিয়োজিত হবে। এক্ষেত্রে বিশেষ করে ইউরোপের নাম উল্লেখ করবার অর্থ এই যে, এশিয়াবাসীদের কতদূর মনুষ্যত্ব আছে না-আছে–এ বৈজ্ঞানিক যুগে তার পরীক্ষা হয় নি। ও খতা হাতে পড়লে বোঝা যেত যে আমরা বাঁদর কি মানুষ।
এই যুদ্ধের বেদনা থেকে ইউরোপের ন্যায়-বুদ্ধি যে জাগ্রত হয়ে উঠবে, তার আর সন্দেহ নেই; কেননা, ইতিমধ্যেই সেদেশে মানুষে ত্রাহি-মধুসূদন বলে চীৎকার করছে, প্রহারেণ-ধনঞ্জয় বলে নয়।
কিন্তু পুরুষমানুষ যে কখনো মানুষ হবে–এ বিশ্বাস লেখিকার নেই। তিনি পুরুষকে ইতিহাসের অতিৰিস্তৃত ক্ষেত্রে দাঁড় করিয়ে দেখিয়েছেন যে, সে কত ক্ষদ্র। এবং ঐরূপে তার ক্ষদ্রত্ব প্রমাণ করে প্রস্তাব করেছেন যে, হয় সে অীধর্ম অবলম্বন করুক, নয় তার শাসনের ভার শ্রীজাতির হাতে দেওয়া হোক। এস্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি স্ত্রীধর্মী হওয়াই পুরুষের পক্ষে মনুষ্যত্বলাভের একমাত্র উপায় হয়, তাহলে আমাদের মেয়েলি ব’লে কেন উপহাস করা হয়েছে। সম্ভবত লেখিকার মতে আমরা প্রজাতির গুণগুলি শিক্ষা করতে পারি নি, শুধু তাদের দোষগুলিই আত্মসাৎ করেছি। আমাদের এটিগুলির অনুকরণ অপরকে করতে দেখলে আমরা সকলেই বিরক্ত হই; কেননা, শ্রদ্ধাপূর্বক ও-কার্য করলেও তা ভ্যাংচানির মতই দেখায়। কিন্তু একথাও সমান সত্য যে, মানুষে অপরের গুণের অনুসরণ করতে পারলেও অনুকরণ শুধু পরের দোষেরই করতে পারে। এর পরিচয় জীবনে ও সাহিত্যে নিত্য পাওয়া যায়। কিন্তু অবস্থার গুণে আমরা কিছু করতে হলেই অনুকরণ করতে বাধ্য। আমরা এক্সপেরিমেন্টের সাহায্যে নিজের জীবন গঠন করতে সাহস পাই নে বলে আমাদের সম্মুখে একটা তৈরি-আদশ থাকা আবশ্যক, যার অনুকরণে আমরা নিজেদের গড়ে নিতে পারি। আমরা এরকম দুটি আদর্শের সন্ধান পেয়েছি : একটি হচ্ছে বর্তমান ইউরোপীয়, অপরটি প্রাচীন হিন্দু। তার উপর যদি আবার শ্রীজাতিকেও আদর্শ করতে হয়, তাহলে এই তিন জাতির দোষ একাধারে মিলিত হয়ে যে চিজ, দাঁড়াবে, জগতে আর তার তুলনা থাকবে না। সৃষ্টি হচ্ছে ত্রিগুণাত্মক, আমরা ত্রিদোষাত্মক হলে যে সৃষ্টিছাড়া হব, তার আর কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং এখন বিবেচ্য তোমাদের হাতে শাসনকর্তৃত্ব দেওয়া কর্তব্য কি না। এতে পৃথিবীর অপর দেশের পুরুষজাতির ক্ষতিবৃদ্ধি কি হবে তা বলতে পারি নে, কিন্তু আমাদের কোনো লোকসান নেই। কারণ আমরা তো চিরদিনই তোমাদের শাসনাধীন রয়েছি। আমাদের দুর্গতির একটি প্রধান কারণও ওই। লেখিকা তো নিজেই স্বীকার করেছেন, স্ত্রীলোকে অশিক্ষার গুণে এদেশের পুরুষ-সমাজকে চালমাৎ করে রেখেছে। আসল কথা, স্ত্রীলোকেরও পুরুষের অধীন থাকা ভালো নয়, পুরুষেরও স্ত্রীলোকের অধীন থাকা ভালো নয়। দাসত্বও মনুষ্যত্বকে যেমন বিকৃত করে, প্রভুত্বও তেমনি করে। স্ত্রীপুরুষ যে অহর্নিশি লড়াই করে তার কারণ, একজন আর-একজনের অধীন। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে, যুদ্ধ ততদিন থাকবে, যতদিন এ পৃথিবীতে একদিকে প্রভুত্ব আর অপরদিকে দাসত্ব থাকবে।
কিন্তু ও ব্যাপার যে পৃথিবীতে আর বেশি দিন থাকবে না, এই যুদ্ধেই তা প্রমাণ হয়ে যাবে। যুদ্ধ আসলে একটি ভীষণ তর্ক বই আর কিছুই নয়। যেবিষয়ের শুধু কাগজে-কলমে মীমাংসা হয় না, তার সময়ে সময়ে হাতেকলমে মীমাংসা করতে হয়। ইউরোপে কামান-বন্দকে যে তর্ক চলছে, তার বিষয় হচ্ছে যুদ্ধ করা উচিত কি অনুচিত। এক্ষেত্রে পবপক্ষ হচ্ছে জর্মানি আর উত্তরপক্ষ হচ্ছে ইংলণ্ড ফ্রান্স বেলজিঅম ইত্যাদি। এক্ষেত্রে যদি উত্তরপক্ষ জয়ী হয় (এবং জয় যে ন্যায়ের অনুসরণ করবে, সেসম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই), তাহলে মানবজাতি এই চড়ান্ত মীমাংসায় উপনীত হবে যে, যুদ্ধ অকর্তব্য। আর-একটি কথা, পুষমানুষে যুদ্ধ-রপ প্রচণ্ড বিবাদ কখনো-কখনন করে, কিন্তু লেখিকার স্বজাতিই হচ্ছে সকল নিত্যনৈমিত্তিক বিবাদের মূল। এর জন্য আমাদের বুদ্ধি কিংবা তাঁদের হদয় দায়ী, তার বিচার আমি করতে চাই নে। আমরা মনসা হতে পারি, কিন্তু ধনোর গন্ধ ওঁরাই যোগান। ওঁরা উসকে দিয়ে পুরুষকে যে পরিমাণে বীরপুরুষ’ করে তুলতে পারেন, তা কোনোও দর্শন-বিজ্ঞানে পারে না। তবে যে লেখিকা শমদম প্রভৃতি সদগুণে নিজেদের বিভূষিত মনে করেন, সে ভুল ধারণার জন্যও দায়ী আমরা। আমি পূর্বে বলেছি যে, শ্রীজাতিকে আমরা সমাজে স্বাধীনতা দিই নি, কিন্তু সাহিত্যে দিয়েছি। এ কাজটি ন্যায় হলেও সেইসঙ্গে একটি অন্যায় কাজও আমরা করেছি। আমাদের সমাজে শ্রীজাতির কোনোরূপ মর্যাদা নেই, কিন্তু সাহিত্যে যথেষ্টর চাইতেও বেশি আছে। এর কারণ, সকল সমাজের উপর হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হলে তোমাদের গণকীর্তন করা ছাড়া আর আমাদের উপায়ান্তর নেই। আমাদের নিজের বিষয় মুখ ফুটে অহংকার করা চলে না; কেননা, আমাদের দেহমনের দৈন্য বিশ্বমানবের কাছে প্রত্যক্ষ: সতরাং আমরা বলতে বাধ্য যে, আমাদের সমাজের সকল ঐশ্বর্য অন্তঃপরের ভিতর চাবি-দেওয়া আছে। এসব কথার উদ্দেশ্য আমাদের নিজের মন-যোগানো এবং পরের মন-ভোলানো। ও হচ্ছে তোমাদের নামে বেনামি করে আমাদের আত্মপ্রশংসা করা। সুতরাং, যদি মনে কর, ওইসব প্রশংসিত গুণে তোমাদের কোনো স্বত্ব জন্মেছে, তাহলে তোমরা যে-তিমিরে আছ, সেই তিমিরেই থাকবে।
কার্তিক ১৩২১
নোবল প্রাইজ
সব জিনিসেরই দুটি দিক আছে–একটি সদর, আর-একটি মফস্বল। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন বলে বহলোক যে খুশি হয়েছেন, তার প্রমাণ তো হাতেহাতেই পাওয়া যাচ্ছে; কিন্তু সকলে যে সমান খুশি হন নি, এ সত্যটি তেমন প্রকাশ হয়ে পড়ে নি। এই বাংলাদেশের একদল লোকের, অর্থাৎ লেখকসম্প্রদায়ের, এ ঘটনায় হরিষে-বিষাদ ঘটেছে। আমি একজন লেখক, সুতরাং কি কারণে ব্যাপারটি আমাদের কাছে গুরুতর বলে মনে হচ্ছে সেইকথা আপনাদের কাছে নিবেদন করতে ইচ্ছা করি।
প্রথমত, যখন একজন বাঙালি লেখক এই পুরস্কার লাভ করেছেন তখন আর-একজনও যে পেতে পারে, এই ধারণা আমাদের মনে এমনি বদ্ধমূল হয়েছে যে, তা উপড়ে ফেলতে গেলে আমাদের বক ফেটে যাবে। অবশ্য আমরা কেউ রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ নই, বড়জোর তাঁর স্বপক্ষ কিংবা বিপক্ষ। তাই বলে পড়তাটা যখন এদিকে পড়েছে তখন আমরা যে নোবেল প্রাইজ পাব না এ হতে পারে না। সাহিত্যের রাজটিকা লাভ করা যায় কপালে। তাই বলছি, আশার আকাশে দোদুল্যমান এই টাকার থলিটি চোখের সম্মুখে থাকাতে লেখাজিনিসটে আমাদের কাছে অতি সকঠিন হয়ে উঠেছে।
স্বর্গ যদি অকস্মাৎ প্রত্যক্ষ হয় আর তার লাভের সম্ভাবনা নিকট হয়ে আসে, তাহলে মানুষের পক্ষে সহজ মানুষের মত চলাফেরা করা অসম্ভব হয়ে আসে, তাহলে মানুষের পক্ষে সহজ মানুষের মত চলাফেরা করা অসম পড়ে। চলাফেরা দরে যাক, তার পক্ষে পা ফেলাই অসম্ভব হয়—এই ভয়ে, পাছে হাতের স্বর্গ পায়ে ঠেলি। তেমনি নোবেল প্রাইজের সাক্ষাৎ পাওয়া অবধি লেখা সম্বন্ধে দায়িত্বজ্ঞান আমাদের এত বেড়ে গেছে যে, আমরা আর হালকাভাবে কলম ধরতে পারি নে।
এখন থেকে আমরা প্রতি ছত্র সুইডিশ অ্যাকাডেমির মুখ চেয়ে লিখতে বাধ্য। অথচ যেদেশে ছমাস দিন আর ছমাস রাত, সেদেশের লোকের মন যে কি করে পাব তাও বুঝতে পারি নে। এইটুকু মাত্র জানি যে, আমাদের রচনায় অর্ধেক আলো আর অর্ধেক ছায়া দিতে হবে; কিন্তু কোথায় এবং কি ভাবে, তার হিসেব কে বলে দেয়। সুইডেন যদি বারোমাস রাতের দেশ হত, তাহলে আমরা নির্ভয়ে কাগজের উপর কালির পোঁচড়া দিয়ে যেতে পারতুম; আর যদি বারোমাস দিনের দেশ হত, তাহলেও নয়, ভরসা করে শাদা কাগজ পাঠাতে পারতুম। কিন্তু অবস্থা অন্যরপ হওয়াতেই আমরা উভয়সংকটে পড়েছি।
দ্বিতীয় মুশকিলের কথা এই যে, অদ্যাবধি বাংলা আর বাঙালিভাবে লেখা চলবে না। ভবিষ্যতে ইংরেজি তরজমার দিকে এক নজর রেখে এক নজর কেন, পরো নজর রেখেই আমাদের বাংলাসাহিত্য গড়তে হবে। অবশ্য আমরা সকলেই দোভাষী, আর আমাদের নিত্য কাজই হচ্ছে তরজমা করা। কিন্তু সব্যসাচী হলেও এক তীরে দুই পাখি মেরে উঠতে পারি নে। আমরা যখন বাংলা লিখি, তখন ইংরেজির তরজমা করি কিন্তু সে না জেনে; আর যখন ইংরেজি লিখি, তখন বাংলার তরজমা করি–সেও না জেনে। কিন্তু এখন থেকে ঐ কাজই আমাদের সজ্ঞানে করতে হবে, মুশকিল ত ঐখানেই। মনোভাবকে প্রথমে বাংলাভাষার কাপড় পরাতে হবে, এই মনে রেখে যে আবার তাকে সে কাপড় ছাড়িয়ে ইংরেজি পোশাক পরিয়ে সুইডিশ অ্যাকাডেমির সম্মুখে উপস্থিত করতে হবে। এবং এর দরুন মনোভাবটির চেহারাও এমনি ত’য়ের করতে হবে যে, শাড়িতেও মানায় গাউনেও মানায়।
এক ভাষাতে চিন্তা করাই কঠিন, কিন্তু একসঙ্গে যুগপৎ দুটি ভাষাতে চিন্তা করাটা অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু কায়ক্লেশে আমাদের সেই অসাধ্যসাধন করতেই হবে। একটি বাঙালি আর-একটি বিলেতি— এই দুটি স্ত্রী নিয়ে সংসার পাতা যে আরামের নয়, তা যাঁরা ভুক্তভোগী নন তাঁরাও জানেন। তাছাড়া, এ উভয়ের প্রতি সমান আসক্তি না থাকলে এ দুই সংসার করাও মিছে। সর্বভূতে সমদৃষ্টি, চাই কি, মানুষের হতেও পারে; কিন্তু দুটি পত্নীতে সমান অনরোগ হওয়া অসম্ভব, কেননা মানুষের চোখ দুটি হলেও হদয় শুধু একটি। স্বৈণ হতে হলে একটিমাত্র স্ত্রী চাই। এমনকি, দুই দেবীকে পুজা করতে হলেও পালা করে ছাড়া উপায়ান্তর নেই। অতএব দাঁড়াল এই যে, বছরের অর্ধেক সময় আমাদের বাংলা লিখতে হবে, আর অর্ধেক সময় ইংরেজিতে তার তরজমা করতে হবে। ফিরেফিরতি সেই সুইডেনের কথাই এল; অর্থাৎ আমাদের চিদাকাশে ছমাস রাত আর ছমাস দিনের সৃষ্টি করতে হবে, অথচ দৈবশক্তি আমাদের কারও নেই।
তৃতীয় মুশকিল এই যে, সে তরজমার ভাষা চলতি হলে চলবে না। সে ভাষা ইংরেজি হওয়া চাই, অথচ ইংরেজের ইংরেজি হলেও হবে না। দেশী আত্মা এমনিভাবে বিলেতি দেহে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া চাই, যাতে তার পবজন্মের সংস্কারটুকু বজায় থাকে। ফুল ফোটাতে হবে বিলেতি, কিন্তু তার গায়ে গন্ধ থাকা চাই দেশী কুড়ির। প্রজাপতি ওড়াতে হবে বিলেতি, কিন্তু তার গায়ে রং থাকা চাই দেশী পোকার। এককথায়, আমাদের পূর্বের সূর্য পশ্চিমে ওঠাতে হবে। এহেন অঘটনঘটনপটিয়সী বিদ্যা অবশ্য আমাদের নেই।
কাজেই যে কার্য আমরা একদিন বাংলায় করতে চেষ্টা করে অকৃতকার্য হয়েছি–রবীন্দ্রনাথের লেখার অনুকরণ— তাই আবার দোকর করে ইংরেজিতে করতে হবে। ইউরোপে আসল জিনিসটি গ্রাহ্য হচ্ছে বলে নকল জিনিসটিও যে গ্রাহ্য হবে, সে আশা দুরাশা মাত্র। ইউরোপ এদেশে মেকি চালায় বলে আমরাও যে সেদেশে মেকি চালাতে পারব–এমন ভরসা আমার নেই।
ফলে, আমরা শাদাকে কালো আর কালোকে শাদা যতই কেন করি নে, আমাদের পক্ষে নোবেল প্রাইজ ছিকেয় তোলা রইল। কিন্তু যদি পাই? বিড়ালের ভাগ্যে সে ছিকে যদি ছেড়ে! সেও আবার বিপদের কথা হবে। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার অর্থ শুধু অনেকটা টাকা পাওয়া নয়, সেইসঙ্গে অনেক খানি সম্মান পাওয়া। অনর্থ এক্ষেত্রে অর্থ নয় কিন্তু তৎসংসষ্ট গৌরবটুকু। বাংলা লিখে আমরা কি অর্থ কি গৌরব, কিছুই পাই নে। বাংলাসাহিত্যে আমরা ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াই, এবং পুরস্কারের মধ্যে লাভ করি তার চাটটকু। স্বদেশীর শুভ-ইচ্ছার ফুলচন্দন কালেভদ্রেও আমাদের কপালে জোটে না বলে ইউরোপ যদি উপযাচী হয়ে আমাদের মাথায় সাহিত্যের ভাইফোঁটা দেয়, তাহলে তার ফলে আমাদের আয়বৃদ্ধি না হয়ে হ্রাস হবারই সম্ভাবনা বেড়ে যায়।
প্রথমেই দেখুন যে, নোবেল প্রাইজের তারের সঙ্গেসঙ্গেই আমরা শত, শত চিঠি পাব। এবং এই অসংখ্য চিঠি পড়তে এবং তার উত্তর দিতেই আমাদের দিন কেটে যাবে, সাহিত্য পড়বার কিংবা গড়বার অবসর আর আমাদের থাকবে না। এককথায় সমাজের খাতিরে, ভদ্রতার খাতিরে, আমাদের সাহিত্যের ফলফল ছেড়ে শুধু শুষ্কপত্র রচনা করতে হবে। এই কারণেই বোধ হয় লোকে বলে যে, নোবেল প্রাইজ লাভ করার অর্থ হচ্ছে সাহিত্যজীবনের মোক্ষ লাভ করা।
আর-এক কথা, টাকাটা অবশ্য ঘরে তোলা যায় এবং দিব্য আরামে উপভোগ করা যায়, কিন্তু গৌরব-জিনিসটে ওভাবে আত্মসাৎ করা চলে না। দেশসুদ্ধ লোক সে গৌরবে গৌরবান্বিত হতে অধিকারী। শাস্ত্রে বলে ‘গৌরবে বহুবচন’; কিন্তু তার কত অংশ নিজের প্রাপ্য, আর কত অংশ অপরের প্রাপ্য সেসম্বন্ধে কোনো-একটা নজির নেই বলে এই গৌরব-দায়ের ভাগ নিয়ে স্বজাতির সঙ্গে একটা জ্ঞাতিবিরোধের সৃষ্টি হওয়া আশ্চর্য নয়। অপরপক্ষে যদি একের সম্মানে সকলে সমান সম্মানিত জ্ঞান করেন, এবং সকলের মনে কবির প্রতি অকৃত্রিম ভ্রাতৃভাব জেগে ওঠে। তাতেও কবির বিপদ আছে। ত্রিশ দিন যদি বিজয়াদশমী হয়, এবং ত্রিশকোটি লোক যদি আত্মীয় হয়ে ওঠেন, তাহলে নররূপধারী একাধারে তেত্রিশকোটি দেবতা ছাড়া আর কারও পক্ষে অজস্র কোলাকুলির বেগ ধারণ করা অসম্ভব। ও অবস্থায় রক্তমাংসের দেহের মুখ থেকে সহজেই এইকথা বেরিয়ে যায় যে ‘ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি’। এবং ওকথা একবার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেলে তার ফলে কবিকে কেঁদে মরতে হবে।
তাই বলি, আমাদের বাঙালি লেখকদের পক্ষে নোবেল প্রাইজ হচ্ছে। দিল্লির লাড্ডু–যো খায়া ওভি পস্তায়া, যো না খায়া ওভি পস্তায়া।
মাঘ ১৩২০
পত্র ১
সম্পাদকমহাশয় সমীপেষু,
আপনি যে নূতন কাগজ বার করেছেন, তার যদি কোনো উদ্দেশ্য থাকে ততা সে হচ্ছে নূতন কথা নূতন ধরনে বলা। এ উদ্দেশ্য সফল করতে হলে নূতন লেখক চাই, নচেৎ সবুজপত্র কালক্রমে শ্বেতপত্রে পরিণত হবে।
যদি আপনি মুখপত্রে ‘আমি’র পরিবর্তে ‘আমরা’ শব্দ ব্যবহার করেছেন, তথাপি ঐ বহুবচনের পিছনে যে বহু লেখক আছেন, তার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। বাংলায় দ্বিবচন নেই, সম্ভবত সেই কারণেই আপনি প্রথমপুরুষের বহুবচন ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ, অদ্যাবধি কেবলমাত্র দুটি লেখকেরই পরিচয় পাওয়া গেছে : এক সম্পাদক, আর-এক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
শ্ৰীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে গুনতির মধ্যে ধরা গেল না; কেননা, আপনারা লেখার যা নমনা দেখিয়েছেন তার থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, আপনার প্রধান ভরসাস্থল হচ্ছে গদ্য। কারণ, সোজা কথা বাঁকা করে এবং বাঁকা কথা সোজা করে বলা পদ্যের রীতি নয়।
আর ছিলুম আমি, কিন্তু আর বেশিদিন যে থাকব কিংবা থাকতে পারব, এমন আমার ভরসা হয় না। হয় আপনি আমাকে ছাড়বেন, নয় আমি আপনাকে ছাড়ব। আমার লেখায়, আর যাই হোক সবুজপত্রের যে গৌরব বৃদ্ধি হয় নি, একথা সর্বসমালোচকসম্মত। এ অবস্থায় ‘বীরবল’ অতঃপর ‘আবল-ফজল’ হওয়া ব্যতীত উপায়ান্তর দেখতে পাচ্ছেন না। ভবিষ্যতে আইন-ই-আঙ্গরেজি নামকু যে নব-বিশ্বকোষ রচনা করব ‘সবুজপত্রে তার স্থান হবে না। যদি ‘ফৈজি’ হতে পারতুম, অহলেও নাহয় আপনার কাগজের জন্য একখানি দেশকালোপযোগী অর্থাৎ স্বয়ংবরা-তিরস্কৃত একখানি নলদমন’ রচনা করতে পারতুম; কিন্তু সে হবার জো নেই। আমাকে আবল-ফজল হতেই হবে। আশা করি, বাংলার নবীন আবল-ফজলদের মধ্যে কেউ-না-কেউ আমার সঙ্গে পেশা বদলে নেবেন; কেননা, সাহিত্যরাজ্যে বীরবলেরও আবশ্যকতা আছে। ইংরেজেরা বলেন, এক কোকিলে বসন্ত হয় না–অর্থাৎ আর পাঁচ-রঙের আর পাঁচটি পাখিও চাই। বাংলাসাহিত্যের উদ্যানে যদি বসন্তঋতু এসে থাকে, তাহলে সেখানে কোকিলও থাকবে, কাঠ-ঠোকরাও থাকবে, লক্ষ্মী-পেঁচাও থাকবে, হতুম-পেচাও থাকবে। মনোরাজ্যে যখন নানা পক্ষ আছে, তখন নানা পক্ষী থাকাই স্বাভাবিক। যেমন এক ‘বউ-কথা-কও’ নিয়ে কবিতা হয় না, তেমনি এক ‘চোখ-গেল’ নিয়ে দর্শনও হয় না।
উপরোক্তভাবে বাদসাদ দিয়ে শেষে দাঁড়াল এই যে, আপনার কাগজের যা প্রধান প্রয়োজন, সেইটিই হচ্ছে তার প্রধান অভাব–অর্থাৎ নূতন লেখক। মনে রাখবেন যে, এদেশে আজকাল খাঁটি সাহিত্য চলবে না; চলবে যা, তা হচ্ছে জাতীয় সাহিত্য। যদিচ একথার সার্থকতা কি, সেসম্বন্ধে কারও স্পষ্ট ধারণা নেই। কোনো লেখা যদি সাহিত্য না হয়, তবুও তার আর মার নেইযদি তা তথাকথিত জাতীয় হয়। এর কারণ, প্রথমত, আমরা বিশেষ্যের চাইতে বিশেষণের অধিক ভক্ত; দ্বিতীয়ত, আমরা সাহিত্য-বিচার করতে পারি-আর-নাপারি, জাত-বিচার করতে জানি। বলা বাহুল্য যে, দু হাতে কখনো জাতীয় সাহিত্য গড়ে তোলা যায় না; দু হাতে অবশ্য তালি বাজে। আপনারা যদি না স্বজাতিকে অহর্নিশি করতালি দিতে প্রস্তুত হতেন, তাহলে আপনাদের হাতে জাতীয় সাহিত্য রচিত হত; কিন্তু সেবিষয়ে আপনাদের যখন তাদশ উৎসাহ দেখা যাচ্ছে না, তখন নূতন লেখক চাই।
বাংলা লেখবার লোকের অভাব না থাকলেও ‘সবুজপত্রে লেখবার লোকের অভাব যে কেন ঘটছে, তার কারণ নির্ণয় করতে হলে বঙ্গসাহিত্যের বর্তমান অবস্থার পর্যালোচনা করা আবশ্যক।
বাংলাসাহিত্যে যে আজ বসন্তকাল উপস্থিত, ‘সবুজপত্রের আবির্ভাব তার একমাত্র প্রমাণ নয়। ইতিপবেই স্বদেশী জ্ঞানবক্ষের নানা ডালপালা বেরিয়েছে, এবং অন্তত তার একটি শাখায় অর্থাৎ ইতিহাসের অক্ষয় শাখায় এমন ফল ফটেছে ও ফল ধরেছে, যা সমালোচকদের নখদন্তের অধিকারবহির্ভূত; কেননা, সে ফল তামার এবং সে ফল পাথরের।
কিন্তু আপনি পাঠকদের এই ফলাহারে নিমন্ত্রণ করেন নি। আপনি সবুজপত্রে যে ফল পরিবেষণ করতে চান, সে জ্ঞানবৃক্ষের ফল নয়, কিন্তু তার চাইতে ঢের বেশি মুখরোচক সংসারবিষবক্ষের সেই ফল, যা আমাদের পর্বপুরুষেরা অমতোপম মনে করতেন। সেই-জাতীয় লেখকেরা হচ্ছেন আপনার মনোমত, যাঁরা কিছুই আবিষ্কার করেন না কিন্তু সবই উম্ভাবনা করেন, যাঁরা বস্তুজগৎকে বিজ্ঞানের হাতে সমর্পণ করে মনোজগতের উপাদান নিয়ে। সাহিত্য গড়েন।
আমাদের সাহিত্যসমাজে কবি-দার্শনিকের ভিড়ের ভিতর বৈজ্ঞানিকদেরই খুঁজে পাওয়া ভার, অতএব আপনার স্বজাতীয় সাহিত্যিকের অভাব এদেশে মমাটেই নেই। তাহলেও তাঁরা যে উপযাচী হয়ে এসে আপনাদের দলে ভিড়বেন, তার সম্ভাবনা কম; কেননা, যাতে করে দল বাঁধে, সেরকম কোনো মতের সন্ধান আপনাদের লেখায় পাওয়া যায় না।
সকল দেশেই মনেরও একটা চলতি পথ আছে। অভ্যাসবশত এবং সংস্কারবশত দলে দলে লোক সেই পথ ধরেই চলতে ভালোবাসে; কারণ মখ্যত সে পথ হচ্ছে জনসাধারণের জীবনযাত্রার পথ। সে পথ মহাজনদের হাতে রচিত হয় নি, কিন্তু লোকসমাজের পায়ে গঠিত হয়েছে। আপনারা বঙ্গসরস্বতীকে সেই পরিচিত পথ ছেড়ে একটি নূতন এবং কাঁচা রাস্তায় চালাতে চান। আপনারা বলেন ‘সম্মখে চল’, কিন্তু বুদ্ধিমানেরা বলেন ‘নগণস্যাগ্রতোগচ্ছে’। আপনাদের মত এই যে, সামাজিক জীবনের পদানুসরণ করা কবি কিংবা দার্শনিকের মনের কাজ নয়। জীবনকে পথ-দেখানোই হচ্ছে সে মনের ধর্ম, অতএব কর্তব্য। সুতরাং আপনাদের দ্বারা উদ্ভাবিত, অপরিচিত এবং অপরীক্ষিত চিন্তামাগে অগ্রসর হতে অনেকেই অস্বীকৃত হবেন। বিশেষত, যখন সে পথের একটা নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থান নেই, যদি-বা থাকে তো সে অলকা বর্তমানভারতের পরপারে অবস্থিত। শুনতে পাই, ইউরোপের সকল স্থূলপথই রোমে যায়। তেমনি এদেশের সকল হাঁটাপথই কাশী যায়। কিন্তু আপনারা যখন বাঙালির মনকে কাশীযাত্রা না করিয়ে সমদ্রযাত্রা করাতে চান, তখন যে নূতন লেখকেরা সবুজপত্র নিয়ে আপনাদের সঙ্গে একপংক্তিতে বসে যাবেন, এরূপ আশা করা বৃথা। সুতরাং আপনাদের সেই শ্রেণীর লেখক সংগ্রহ করতে হবে, যাদের কাছে আপনাদের সাহিত্য অচল নয়। এ দলের বহু লোক আপনার হাতের গোড়াতেই আছে।
গত বৈশাখমাসের ‘ভারতী’-পত্রিকাতে আপনি বিলেতফেরত বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। প্রাচীন ব্রাহরণসমাজে এ সম্প্রদায়ের স্থান নেই, সতরাং নূতন ব্রাহরণসমাজ অর্থাৎ সাহিত্যসমাজে এদের তুলে নেওয়া হচ্ছে আপনার পক্ষে কর্তব্য। অতীতের উদ্ধারের পাল্টাজবাবু দিতে হলে পতিতের উদ্ধার করা আবশ্যক।
বিলেতফেরতদের লেখায়, আর-কিছু থাক আর না-থাক, নূতনত্ব থাকবেই। মাইকেল দত্ত, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এই তিনটি বিলেতফেরত কবির ভাষায় ও ভাবে এতটা অপূর্বতা ছিল যে, আদিতে তার জন্য এদের দুজনকে পুরাতনের কাছে অনেক ঠাট্টাবিদ্রূপ সহ্য করতে হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে যে কেউ ঠাট্টা করেন নি, তার কারণ, তিনি সকলকে ঠাট্টা করেছেন। এই থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, বিলেতফেরতের হাতে পড়লে বঙ্গসাহিত্যের চেহারা ফিরে যায়।
আসল কথা, এ যুগের বঙ্গসাহিত্য হচ্ছে বিলেতি ঢঙের সাহিত্য। যে হিসেবে দাশরথি রায়ের পাঁচালি ও গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা খাঁটি বাংলাসাহিত্য, সে হিসেবে নবসাহিত্য খাঁটি বঙ্গসাহিত্য নয়। এর জন্যে কেউ-কেউ দুঃখও করেন। চোখের জল ফেলবার কোনো সুযোগ বাঙালি ছাড়ে না। ব্যাস-বাল্মীকির জন্যও আমরা যেমন কাঁদি, পাঁচালিওয়ালাদের জন্যও আমরা তেমনি কাঁদি। কিন্তু সমালোচকেরা চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়ে দিলেও বগসরস্বতী আর গোবিন্দ-অধিকারীর অধিকারভুক্ত হবেন না, এবং দাশরথিকেও সারথি করবেন না।
আমাদের নবসরস্বতী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিতা, এবং কলেজে-শিক্ষিত লোকেরাই অদ্যাবধি তাঁর সেবা করে আসছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন; কেউ ফোঁটা কেটে, কেউ হ্যাট পরে। এই প্রভেদের কারণ নির্দেশ করছি। পরোকালে যখন ক্ষত্রিয়েরা একসঙ্গে সরা এবং সোম পান করতেন, তখন ব্রাহণেরা এই শান্তি-বচন পাঠ করতেন :
‘অহে সুরা ও সোম, তোমাদের জন্য দেবগুণ পথক পথক রুপে স্থান কল্পনা করিয়াছেন। তুমি তেজস্বিনী সরা, আর ইনি রাজা সোম, তোমরা আপন আপন স্থানে প্রবেশ কর।’
আমরাও কলেজে যুগপৎ ইংরেজি-সরা এবং সংস্কৃত-সোম পান করেছি। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দুটি পাকস্থলী না থাকায় সেই সুরা আর সোম আমাদের উদরস্থ হয়ে পরস্পর লড়াই করছে। আমাদের সাহিত্য সেই কলহে মুখরিত হয়ে উঠেছে। আমাদের যে নেশা ধরেছে, সে মিশ্র-নেশা। তবে কোথাও-বা তাতে সুরার তেজ বেশি, কোথাও-বা সোমের। মনোজগতে যে আমরা সকলেই বিলেতফেরত, এইকথাটা মনে রাখলে সাহিত্যমন্দিরে আপনার সম্প্রদায়কে প্রবেশ করতে সাহিত্যের পাণ্ডারা আর বাধা দেবেন না, বরং উৎসাহই দেবেন; কেননা, আমরা সকলেই ইংরেজিসাহিত্যে শিক্ষিত, আপনারা উপরন্তু ইংরেজিসভ্যতায় দীক্ষিত।
সামাজিক হিসেবে বিলেতফেরতদের এই গরগেহবাসের ফল যাই হোক, সাহিত্য হিসেবে এর ফল ভালো হবারই সম্ভাবনা। কারণ ইংরেজি-জীবনের সঙ্গে ইংরেজিসাহিত্যের সম্বন্ধ অতিঘনিষ্ঠ। ইংরেজি-জীবনের সঙ্গে যাঁর সাক্ষাৎ-পরিচয় আছে, তিনি জানেন যে, ইউরোপে সাহিত্য হচ্ছে জীবনের প্রকাশ ও প্রতিবাদ; আর সে পরিচয় যাঁর নেই, তিনি ভাবেন যে ও শুধু বাদানুবাদ। সাহিত্যের ভাষ্য ও টীকা জীবনসুত্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লে তা শুধু কথার কথা হয়ে ওঠে। সেই কারণে নবশিক্ষিতসম্প্রদায়ের জীবনে ইংরেজি-জীবনের প্রভাব যে পরিমাণে কম, তাঁদের রচিত সাহিত্যে ইংরেজি-কথার প্রভাব তত বেশি। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমাদের স্বদেশী বক্তৃতায় ও লেখায় নিত্য পাওয়া যায়। সংস্কৃতভাষার ছদ্মবেশ পরিয়েও বিলেতি মনোভাবকে আমরা গোপন করে রাখতে পারি নে। বিদেশী ভাবকে আমি অবশ্য মন থেকে বহিস্কৃত করে দেবার প্রস্তাব করছি নে, কারণ যেসকল ভাব সাত-সমুদ্র-তেরো-নদীর পার থেকে উড়ে এসে আমাদের মনোজগতে জড়ে বসেছে, তাদের বেবাক উপড়ে ফেলা সম্ভব নয়, এবং সম্ভব হলেও তাতে মন উজাড় হয়ে যাবে। তবে যা জালে ওঠে তাই যেমন মাছ নয়, তেমনি যা ভুই ফড়ে ওঠে তাই গাছ নয়। বিলেতিজীবনে বিলেতিসাহিত্য যাচাই করে নিতে না পারলে এই বিদেশী ভাবের জঙ্গলের মধ্যে থেকে সাহিত্যের উদ্যান গড়ে তুলতে পারব না। এই পরখ করবার কাজটি সম্ভবত বিলেতফেরতেরাই ভালো করতে পারবেন।
তবে সাহিত্যসমাজে প্রবেশ করতে এরা সহজে স্বীকৃত হবেন না। লিখতে অনুরোধ করবামাত্র এরা উত্তর করবেন যে, আমরা বাংলা লিখতে জানি নে। কিন্তু ওকথা শুনে পিছপাও হলে চলবে না। সেকেলে বিলেতফেরতেরা বলতেন যে, তাঁরা বাংলা বলতে পারেন না। অথচ সে বিনয় কিংবা সে স্পর্ধা যে সত্য নয়, তার প্রমাণ আজ বিলেতফেরতের মুখে-মুখে পাওয়া যায়। হতে পারে যে, বাংলা লিখতে পারি নে–একথা বলায় প্রমাণ হয় যে, বক্তা ইংরেজি লিখতে পারেন। অথচ এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, যে লেখা সাহিত্য বলে গণ্য হতে পারে, সে ইংরেজি কোনো দেশী লোক লিখতে পারেন না। যাঁরা আদালতে এবং সভাসমিতিতে ইংরেজিভাষায় ওকালতি এবং ‘কলাবতী’ করেন, তাঁরা যে ওভাষায় শুধু পড়া মুখস্থ দেন তা শ্রোতামাত্রেই বুঝতে পারে। আমরা আইন সম্বন্ধে এবং রাজনীতি সম্বন্ধে ইংরেজরাজপুরুষের কাছে নিত্য পরীক্ষা দিতে বাধ্য, সুতরাং ও-ই ক্ষেত্রে মুখস্থবিদ্যা যার যত বেশি সে তত বড়-বড় প্রাইজ পায়; কিন্তু তার থেকে এ প্রমাণ হয় না যে, ঐ প্রাইজের দৌলতে তাঁরা ইংরেজিসাহিত্যসমাজে প্রোমোশন পান। সুতরাং সাহিত্যবস্তু যে কি, তা যিনি জানেন তাঁকে ইংরেজি ত্যাগ করে বাংলা লেখাতে প্রবত্ত করতে কিঞ্চিৎ সাধ্য-সাধনার আবশ্যক হবে। বিলেতি বট ত্যাগ করলে বঙ্গসন্তান যে স্বদেশের সাহিত্যক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতে পারেন, সেবিষয়ে আমার সন্দেহ নেই; তবে বট ছেড়ে যদি পণ্ডিতি-খড়ম পরে বেড়াতে হয়, তাহলে অবশ্য আরও বিপদের কথা হবে। কিন্তু বঙ্গসরস্বতীর মন্দিরে খোলাপায়ে প্রবেশ করাটাই যে কর্তব্য এবং শোভন, সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই সেটি বোঝা উচিত। অবশ্য পণ্ডিতি-খড়মের প্রধান গুণ এই যে, তা যত বেশি খটখটায়মান হবে, লোকে তত ‘সাধু, সাধু’ বলবে। কিন্তু এটি মনে রাখা উচিত যে, আশৈশব ওবস্তুর ব্যবহারে অভ্যস্ত না হলে খড়মধারীদের পদে-পদে হোঁচট খাওয়া অনিবার্য।
বিলেতফেরতকে লেখক তৈরি করার প্রধান বাধা হচ্ছে যে, তাঁরা অধিকাংশই আইনব্যবসায়ী। উকিল ও কোকিল হচ্ছে বিভিন্ন শ্রেণীর জীব, যদিচ উভয়েই বাচাল। এর এককে দিয়ে অপরের কাজ করানো যায় না। তবে কথা হচ্ছে এই যে, যে লঙ্কায় যায় সেই যেমন রাক্ষস হয়ে ওঠে, তেমনি যে আদালতে যায় সেই যে রাসবিহারী হয়, তা নয়। সকলেই জানেন যে, এদেশের কত বিদ্যাবুদ্ধি আদালতের মাঠে মারা যাচ্ছে। তার কারণ, ও শুষ্ক এবং কঠিন ক্ষেত্রের রস আত্মসাৎ করা দুরে থাকুক, অনেকের মন তাতে শিকড়ও গাড়তে পারে না। এ অবস্থায় যে অনেকে আদালতের মাটি কামড়ে পড়ে থাকেন, তার কারণ ও-স্থান ত্যাগ করলে হাঁসপাতালে যাওয়া ছাড়া এদেশে স্বাধীন ব্যবসায়ীর আর গত্যন্তর নেই। তাই নিত্যই দেখতে পাওয়া যায়, বহু বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোক এক ফোঁটা জল না খেয়ে দিনের পর দিন ন্যৰ্জশিরে কুঞ্জপঠে অগাধ আইনের পুস্তকের ভার বহন করে আদালতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সে গরেভারে পঠদণ্ড ভঙ্গ হলেও যে তাঁরা পষ্ঠভঙ্গ দেন না, তার আর-একটি কারণ এই যে, এই মরুভূমিতে তাঁরা নিত্য রজতমায়ার মরীচিকা দেখেন। সুতরাং এই আইনের দেশ একবারে ত্যাগ করতে কেউ রাজি হবেন না; তবে মধ্যমধ্যে সবুজপত্রের ওয়েসিসে এসে বিশ্রামলাভ করতে এদের আপত্তি না-ও হতে পারে। আপনি শুধু এইটুকু সতর্ক থাকবেন যে, এমন লোক আপনার বেছে নেওয়া চাই যার মন ইংরেজের আইনের নজিরবন্দী হয় নি।
আমার শেষকথা এই যে, যেন-তেন-প্রকারেণ আপনার নিজের দলের লোককে, আর-কোনো কারণে না হোক— আত্মরক্ষার জন্যও, আপনাকে লেখক তৈরি করে নিতে হবে; কারণ তাঁরা যদি লেখক না হন, তাহলে তাঁরা সব সমালোচক হয়ে উঠবেন। ইতি।
শ্রাবণ ১৩২১
পত্র ২
শ্ৰীযুক্ত ‘সবুজপত্র’সম্পাদকমহাশয় সমীপেষু
সম্প্রতি শ্ৰীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় আবিষ্কার করেছেন যে, এদেশে মাসিকপত্রের পরমায়ু গড়ে চার বৎসর।
ত্রিবেদীমহাশয় বাংলার একজন অগ্রগণ্য আয়ুর্বেদী, ইংরেজিতে যাকে বলে বায়োলজিস্ট–অতএব আয় সম্বন্ধে তাঁর গণনা যে নির্ভুল, একথা আমরা মেনে নিতে বাধ্য।
এই হিসেবে সবুজপত্রের জীবনের মেয়াদ আরও দু বৎসর আছে। এস্থলে বিধির নিয়ম লঙ্ঘন করা অকর্তব্য মনে করেই সম্ভবত আপনারা সবুজপত্রের পবনিদিষ্ট মেয়াদ বাড়িয়ে দেবার জন্য কৃতসংকল্প হয়েছেন। এ পত্র যে দু বৎসরের কড়ারে বার করা হয়, সেবিষয়ে আমি সাক্ষি দিতে পারি। কেননা, যেক্ষেত্রে সবুজপত্র প্রকাশ করবার ষড়যন্ত্র করা হয়। মনে রাখবেন হাল আইনে দজনেও ষড়যন্ত্র হয় সেক্ষেত্রে আমি সশরীরে উপস্থিত ছিলুম।
সবুজপত্র আর-এক বৎসর সবুজ থাকবে, এ সংবাদে পাঠকসমাজ খুশি হবেন কি না জানি নে, কিন্তু সমালোচকসম্প্রদায় যে হবেন না— সেবিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কেননা, এরা ও-পত্রের রং কিংবা রস, দুয়ের কোনোটিই পছন্দ করেন না। এদের মতে সবুজপত্র সাহিত্যের তেজপত্র, যতক্ষণ না তার রং ও রস দুইই লোপ পায় অর্থাৎ যতক্ষণ না তা শুকিয়ে যায়, ততক্ষণ তা বাঙালি পুরুষের মুখরোচকও হবে না, বঙ্গরমণীর গৃহস্থালির কাজেও লাগবে না। সবুজপত্র তেজপত্র কি না জানি নে কিন্তু তা যে নিস্তেজ পত্র নয়, তার প্রমাণ উত্তেজিত সমালোচনায় নিত্যই পাওয়া যায়।
এক্ষেত্রে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন যে, সবুজপত্রের বেচে থাকবার কিংবা ও-পত্ৰকে বাঁচিয়ে রাখবার আবশ্যকতাই বা কি আর সার্থকতাই বা কোথায়, তাহলে তার কোনো উত্তর দেবেন না। কেননা, ও প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই।
এ পৃথিবীতে বাঁচবার এবং বাঁচিয়ে রাখবার পক্ষে কোনোরূপ যুক্তি নেই; অপরপক্ষে মরবার এবং মারবার পক্ষে এত বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক যুক্তি আছে যে, তার ইয়ত্তা করা যায় না। পৃথিবীর সকল দেশের সকল শাস্ত্রই মানুষকে মরবার জন্য প্রস্তুত হতে শিক্ষা দেয়; যে চিন্তার উপর মৃত্যুর ছায়া পড়ে নি, তাকে আমরা গভীরও বলি নে, উচ্চও বলি নে। এ জড়বিশ্বের অন্তরে প্রাণ-জিনিসটি প্রক্ষিপ্ত। দর্শন-বিজ্ঞানের পাকা-খাতায় প্রাণের অঙ্কটা একেবারেই ফাজিল, সুতরাং এ অঙ্কটা বেড়ে গেলে দুনিয়ার জ্ঞানের হিসেবটা আগাগোড়া গরমিল হয়ে যাবে। অতএব যতদিন প্রাণের বিলয় না হয়, ততদিন একটা প্রলয়ের সম্ভাবনা থেকে যাবে। বিশ্বের সম্বন্ধে যা সত্য, সমাজের সম্বন্ধেও তাই সত্য; কেননা, যাকে আমরা মানবসমাজ বলি, সে তো জীবজগতের একটি অংশমাত্র এবং জীবজগৎ এই জড়জগতের একটি ক্ষদ্রাদপিক্ষদ্র অঙ্গমাত্র। সুতরাং একাগ্রমনে মৃত্যুর চর্চা করাতেই মানুষে তার সামাজিক বুদ্ধির পরিচয় দেয়। হত্যা করবার স্বপক্ষে কত হিতকর এবং অখণ্ডনীয় যুক্তি আছে, তার পরিচয় বর্তমান জর্মানির সামরিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। সেদেশে যদি কেউ বলেন যে, অহিংসা পরম ধর্ম, তাহলে তাঁর কথা সভ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহধরূপে গণ্য হবে। অপরপক্ষে, এদেশে যদি কেউ বলেন ‘স্বহিংসা পরম অধম তাহলে তাঁর কথাও সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহধরূপে গণ্য হবে।
বলা বাহুল্য যে, আমাদের দেহের মত আমাদের মনের মধ্যেও প্রাণ আছে। কারণ দেহ-মন একই সত্তার এপিঠ আর ওপিঠ। সৃষ্টিকে যদি কেউ উলটে ফেলতে পারেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে, তখন মন হবে বহির্জগৎ আর দেহ হবে অন্তর্জগৎ। বিশ্বটাকে উলটো করে পড়বার চেষ্টা যে অতিবুদ্ধিমান লোকে নিত্যই করে থাকে, তার প্রমাণ দেশী ও বিদেশী দর্শনে নিত্যই পাওয়া যায়। সে যাই হোক, প্রাণ যে মানুষের অন্তরে আছে শুধু তাই নয়, ও-বন্তু অন্য কোথায়ও নেই; বাহিরে যা আছে, সে শুধু প্রাণের লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনা। যে বস্তুর প্রাণ আছে, তা মৃত্যুর অধীন। সুতরাং মনোজগতেও আমরা হত্যা এবং আত্মহত্যা দুইই করতে পারি এবং করেও থাকি। মনোজগতে মারবার যন্ত্রও কথা, আর বাঁচাবার মন্ত্রও কথা। দেশকালপাত্রভেদে কেউ-বা কথার রপোর কাঠি কেউ-বা তার সোনার কাঠি ব্যবহারের পক্ষপাতী। এ রাজ্যেও জীবনের স্বপক্ষে কিছু বলবার নেই, কারণ এখানেও যত সযুক্তি সব মরণকে বরণ করেছে। সত্যকথা বলতে গেলে, প্রাণের বিরুদ্ধে মানুষের ঢের নালিশ আছে। প্রথমত, প্রাণের ধর্মই হচ্ছে জগতের শান্তি ভঙ্গ করা। পঞ্চপ্রাণ পঞ্চভূতের সঙ্গে অবিশ্রান্ত লড়াই করে এ পৃথিবীতে গাছপালা ফলফল জীবজন্তু প্রভৃতি যা-কিছু, সৃষ্টি করেছে, সে সবই পরিবর্তনশীল; প্রতি মুহতেই সেসকলের ভিতর-বার দুয়েরই কিছু-না-কিছু বদল হচ্ছে। যার ভিতর স্থিতি নেই তার ভিতর উন্নতি থাকতে পারে, কিন্তু শান্তি নেই। দ্বিতীয়ত, এ পৃথিবীতে প্রাণ যে শুধু প্রক্ষিপ্ত তাই নয়, তা ঈষৎ ক্ষিপ্তও বটে। জড়বস্তু যেভাবে জড়জগতের নিয়ম মেনে চলে, প্রাণ প্রাণীর হাতে-গড়া বাগ সেভাবে মানে না। প্রাণ নিত্য নূতন আকারে দেখা দেয়, প্রাণের প্রতি মতির ভিতর কিছু-না-কিছু, বিশেষত্ব আছে–পৃথিবীতে এমন দুটি পাতা নেই, যা এক-ছাঁচে ঢালা। ব্যক্তিত্বেই প্রাণীজগতের পরিচয়। তার পর, প্রাণ যত পরিপুষ্ট হয়, তত তার ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এই ব্যক্তিত্ব নষ্ট করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রাণকে নষ্ট করা। প্রাণ এতই অবাধ্য ও বেয়াড়া যে, মানুষকে ও-বস্তু নিয়ে দিবারাত্র জালাতন হতে হয়। আসলে ও-বস্তু হচ্ছে জড়জগতের বুকের জলা–যেমন আলো তার গায়ের জালা। এরূপ হবারও কারণ আছে। জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক লর্ড কেলভিন আবিষ্কার করেছেন যে, আদিতে পৃথিবীতে প্রাণ ছিল না, কোনো অজানা অতীতের কোনো-এক অশুভ মহতে কোনো অজানা অতিপৃথিবী থেকে প্রাণ শন্যপথে উল্কাযোগে মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হয়। প্রাণের সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এই জড়পৃথিবীর অন্তরে যে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, সে আগুন দেশে-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এবং নানা বস্তুর ভিতর দিয়ে নানা আকারে নানা বর্ণে নানা ভঙ্গিতে জলে উঠেছে। জড়জগৎ এ আগুন নেবাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেও সম্পূর্ণ কৃতকার্য হতে পারছে না।
আমাদের মনোজগতে প্রাণ যে কোথা থেকে এল, সে সন্ধান আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। অনেকের ধারণা, এদেশে ও-বস্তু বিলেত থেকে এসেছে। কিন্তু ইতিপূর্বেও এদেশে যে প্রাণ ছিল, তার প্রমাণ আছে। আমার বিশ্বাস, কোনো অতি-মনোজগৎ থেকে কোনো মানসী-উল্কার কন্ধে ভর করে প্রাণ মানুষের মনের মধ্যে প্রবেশ করেছে। যাঁর মনের ভিতর কখনো নূতন প্রাণের আবির্ভাব হয়েছে, তিনিই জানেন যে, সে প্রাণ উল্কার মত আসে; অর্থাৎ হঠাৎ এসে পড়ে, আর তার দীপ্ত আলোকে সমস্ত মনটাকে উদ্দীপ্ত উত্তপ্ত করে তোলে। গ্যেটে বলেছেন যে, মানুষের মনে নূতন ভালোবাসার সঙ্গেসঙ্গেই নূতন জীবন জন্মলাভ করে। আর ভালোবাসা যে উল্কার মত আমাদের মনের উপর এসে পড়ে, এ সত্য সকলেই জানেন। সুতরাং একটা আকস্মিক উপদ্রবের মত প্রাণের আবির্ভাব হয়। এবিষয়ে হদয় ও মস্তিষ্ক সমধমী। এ জগতে আমরা যাকে সত্য বলি, তাও কোনো অজানা দেশ থেকে অকস্মাৎ এসে সমগ্র অন্তলোককে আলোকিত করে আবির্ভূত হয়। খড়ি পেতে গণনা করে অদ্যাবধি কোনো দার্শনিক কিংবা বৈজ্ঞানিক কোনো সত্যই আবিষ্কার করতে পারেন নি। এবং যে সত্যের ভিতর প্রাণের আগুন আছে, তা মিথ্যাকে জালিয়ে-পুড়িয়ে খায়। সুতরাং একের আবিষ্কৃত সত্যের জালা বহলোককে সহ্য করতে হয়। এবং মানবমনের যে অংশ জড়, সে অংশ মনের এই প্রক্ষিপ্ত ক্ষিপ্ত ও দীপ্ত আগুনকে নেবাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেও সম্পূর্ণ কৃতকার্য হতে পারে নি।
মানুষের ভিতরে-বাইরে জড়ের ও প্রাণের অহর্নিশি যে দ্বন্দ্ব চলছে, সে দ্বন্দ্বের তিলমাত্র বিরাম নেই, ক্ষণমাত্র বিচ্ছেদ নেই। এ যুদ্ধের শেষফল কি দাঁড়াবে, বিশ্বের শেষকথা মৃত্যু কি অমৃতত্ব, সেকথা যাঁর বিশ্ব তিনিই জানেন–তুমিও জান না, আমিও জানি নে। তবে প্রাণের কথা হচ্ছে এই যে, যতক্ষণ বাস ততক্ষণ আশ। আর তার হতাশ হয়ে মাঝপথে শুয়ে পড়বার আজও কোনো কারণ ঘটে নি। কেননা, ক্ষীণ নবীন তৃণাঙ্কুর আজও পৃথিবীর প্রাচীন কঠিন বুক ফড়ে সবুজ হয়ে উঠছে। প্রাণের শক্তি এতই অদম্য যে, এক দেশে তাকে মাটিচাপা দিলে আর-এক দেশে তা ঠেলে ওঠে, এক যুগে তাকে নিবিয়ে দিলে আর-এক যুগে তা জলে ওঠে।
মনোজগতের এই জীবন-মরণের লড়াইয়ের লিপিবদ্ধ ইতিহাসের নামই সাহিত্য। এক্ষেত্রে কে কোন দিক নেবেন, তা তাঁর কোন পক্ষের উপর আস্থা বেশি— তার উপর নির্ভর করে।
আমি পূর্বেই বলেছি যে, বাঁচবার আবশ্যকতা কি, এবং বাঁচবার সার্থকতা কোথায় তা কেউ বলতে পারেন না। তবে যার প্রাণ আছে, তার পক্ষে সেই প্রাণ রক্ষা করবার প্রবত্তি এতই স্বাভাবিক যে, হাজারে ন-শ-নিরানব্বইটি প্রাণী বিনা কারণে প্রাণপণে প্রাণধারণ করতে চায়। প্রাণীমাত্রেরই প্রাণের প্রতি এই অহেতুকী প্রীতিই তার স্থায়িত্বের কারণ। যার এককালে প্রাণ ছিল, তা যে একালে মরেও মরে না— তার পরিচয় লাভ করবার জন্য আমাদের দেশান্তরে যেতে হয় না।
সুতরাং সবুজপত্র যে জীবনের মেয়াদ বাড়িয়ে নিতে স্থিরসংকল্প হয়েছে, তার জন্য কোনো প্রাণীর নিকট আপনার কোনোরূপ জবাবদিহি নেই।
বেচে থাকবার স্বপক্ষে কোনোরূপ যুক্তি না থাকলেও, তার পিছনে প্রকৃতি আছে। কিন্তু বাঁচাবার পক্ষে যুক্তিও নেই, প্রকৃতিও নেই।
আমরা যাকে বলি প্রাণধারণ করা, বৈজ্ঞানিকেরা তাকে বলেন, জীবনসংগ্রাম। তাঁদের মতে প্রাণের প্রধান শত্র, প্রাণী। একের পক্ষে বাঁচতে হলে অপরকে মারা দরকার। সতরাং অপরকে বাঁচিয়ে নিজে বাঁচবার চেষ্টাটি পাগলামি মাত্র। আপনি যদি এ মতে বিশ্বাস করেন, তাহলে আপনি কোননা জিনিসকে বাঁচিয়ে তোলবার কথা মুখে আনবেন না, নইলে সবুজপত্রের কপালে অকালমৃত্যু এবং অপমৃত্যু একই সঙ্গে দুইই ঘটতে পারে।
ইহলোক যে একটা যুদ্ধক্ষেত্র, একথা আমিও মানি; কিন্তু আমার মতে প্রাণের সঙ্গে প্রাণের কোনো ঝগড়া নেই। সংগ্রামটা হচ্ছে আসলে জীবনের সঙ্গে মরণের। সুতরাং নির্বিবাদে বেচে থাকবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ও-দয়ের মধ্যে একটা আপোসে মীমাংসা করে নেওয়া। অতএব সবুজপত্রকে যদি জীবন্মত করতে পারেন, তাহলে তার পরমায়ু, অখণ্ড হবে। আধমরা সরস্বতীই যে লক্ষ্মী, একথা তো এদেশে সর্ববাদিসম্মত। ও-পত্রকে নিজীব করবার জন্য কোনোরূপ আয়াস করতে হবে না, সে আপনিই হবে। কেননা, যাঁর স্পর্শে সবজেপত্র সরস ও সজীব হয়ে উঠেছিল, সেই রবীন্দ্রনাথ জাপানপ্রস্থ অবলম্বন করেছেন।
বৈশাখ ১৩২৩
প্রত্নতত্ত্বের পারশ্য-উপন্যাস
ভারতবর্ষের যে কোনো ভবিষ্যৎ নেই, সেবিষয়ে বিদেশীর দল ও স্বদেশীর দল উভয়েই একমত। আমাদের মধ্যে দুই শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা ভবিষ্যৎ নিয়ে কারবার করেন : এক, যাঁরা রাজ্যের সংস্কার চান; আর-এক, যাঁরা সমাজের সংস্কার চান। বর্তমানকে ভবিষ্যতে পরিণত করতে হলে তার সংস্কার অর্থাৎ পরিবর্তন করা আবশ্যক। এই নিয়েই তো যত গোল। যা আছে তার বদল করা যে রাজ্যশাসনের পক্ষে ক্ষতিকর, এই হচ্ছে রাজ্যশাসকদের মত; আর যা আছে তার বদল করা যে সমাজশাসনের পক্ষে ক্ষতিকর, এই হচ্ছে সমাজশাসিতদের মত। অতএব দেখা গেল যে, ভারতবর্ষের যে ভবিষ্যৎ নেই এবং থাকা উচিত নয়–এ সত্য ইংরেজি ও সংস্কৃত উভয় শাস্ত্রমতেই প্রতিপন্ন হচ্ছে।
২.
ভবিষ্যৎ না থাক, গতকল্য পর্যন্ত ভারতবর্ষের অতীত বলে একটা পদার্থ ছিল; শুধু ছিল বলে ছিল না আমাদের দেহের উপর, আমাদের মনের উপর তা একদম চেপে বসে ছিল। কিন্তু আজ শুনছি, সে অতীত ভারতবর্ষের নয়, অপর দেশের। একথা শুনে আমরা সাহিত্যিকের দল বিশেষ ভীত হয়ে পড়েছি। কেননা, এতদিন আমরা এই অতীতের কালিতে কলম ডুবিয়ে বর্তমান সাহিত্য রচনা করছিলাম। এই অতীত নিয়ে, আমাদের ভিতর যাঁর অন্তরে বীররস আছে তিনি বাহ্বাস্ফোটন করতেন, যাঁর অন্তরে করণরস আছে তিনি ক্রন্দন করতেন, যাঁর অন্তরে হাস্যরস আছে তিনি পরিহাস করতেন, যাঁর অন্তরে শান্তরস আছে তিনি বৈরাগ্য প্রচার করতেন, আর যাঁর অন্তরে বীভৎসরস আছে তিনি কেলেংকারি করতেন। কিন্তু অতঃপর এই যদি প্রমাণ হয়ে যায় যে, ভারতবর্ষের অতীত আমাদের পৈতৃক ধন নয়, কিন্তু তা পরের তাহলে সে ধন নিয়ে সাহিত্যের বাজারে আমাদের আর পোন্দারি করা চলবে না। এককথায়, ইতিহাসের পক্ষে যা পোেষ-মাস, সাহিত্যের পক্ষে তা সর্বনাশ।
৩.
আমাদের এতকালের অতীত যে রাতারাতি হস্তান্তরিত হয়ে গেল, সেও আমাদের অতিবুদ্ধির দোষে। এ অতীত যতদিন সাহিত্যের অধিকারে ছিল, ততদিন কেউ তা আমাদের হাত ছাড়িয়ে নিতে পারে নি। কিন্তু সাহিত্যকে উচ্ছেদ করে বিজ্ঞান অতীতকে দখল করতে যাওয়াতেই আমরা ঐ অমূল্য বস্তু হারাতে বসেছি। সকলেই জানেন যে, ভারতবর্ষের অতীত থাকলেও তার ইতিহাস ছিল না। কাজেই এই অতীতের শাদা কাগজের উপর আমরা এতদিন স্বেচ্ছায় এবং স্বচ্ছন্দচিত্তে আমাদের মনোমত ইতিহাস লিখে যাচ্ছিলম। ইতিমধ্যে বাংলায় একদল বৈজ্ঞানিক জন্মগ্রহণ করে সে ইতিহাসকে উপন্যাস বলে হেসে উড়িয়ে দিয়ে এমন ইতিহাস রচনা করতে কৃতসংকল্প হলেন, যার ভিতর রসের লেশমাত্র থাকবে না থাকবে শুধু বহুতলতা। এরা আহেলা বিলেতি শিক্ষার মোহে একথা ভুলে গেলেন যে, অতীতে হিন্দুর প্রতিভা ইতিহাসে নয় পরাণে, বিজ্ঞানে নয় দর্শনে, ফুটে উঠেছিল। অতীতের মর্মগ্রহণ করে তার চর্ম গ্রহণ করতে যাওয়াতেই সে দেশত্যাগী হতে বাধ্য হল। এতে তাঁদের কোনো ক্ষতি নেই, মধ্যে থেকে সাহিত্য শুধু দেউলে হয়ে গেল। বিজ্ঞানের প্রদীপ যে সাহিত্যের লালবাতি— একথা কে না জানে।
৪.
আমরা সাহিত্যিকের দল অতীতকে আকাশ হিসেবে দেখতুম, অর্থাৎ আমাদের কাছে ও-বস্তু ছিল একটি অখণ্ড মহাশূন্য। সুতরাং সেই আকাশে আমরা কল্পনার সাহায্যে এমন-সব গিরি-পরী নির্মাণ করে চলেছিলুম, যার ত্রিসীমানার ভিতর বিজ্ঞানের গোলাগুলি পৌঁছয় না। বাংলার নবীন প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে এ কার্যটি অকার্য বলেই স্থির হল; কেননা, বৈজ্ঞানিক-মতে ইতিহাস গড়বার জিনিসও নয়, পড়বার জিনিসও নয়— শুধু ঢোঁড়বার জিনিস। সুতরাং ও-জিনিসের অন্বেষণ পায়ের নীচে করতে হবে–মাথার উপরে নয়। যাঁরা আবিষ্কার করতে চান, তাঁদের কর্মক্ষেত্র ভূলোক, দ্যুলোক নয়; কেননা, আকাশদেশ তো স্বতঃআবিষ্কৃত।
এই কারণে, সক্রেটিস যেমন দর্শনকে আকাশ থেকে নামিয়ে মাটির উপরে এনে ফেলেছিলেন, আমাদের বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকেরাও তেমনি ভারতবর্ষের ইতিহাসকে আকাশ থেকে পেড়ে মাটির নীচে পুতে ফেলেছেন।
৫.
এ দলের মতে ভারতবর্ষের অতীত পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হলেও পঞ্চভূতে মিশিয়ে যায় নি; কেননা, কাল অতীতের অগ্নিসৎকার করে না, শুধু তার গোর দেয়। এককথায়, অতীতের আত্মা স্বর্গে গমন করলেও তার দেহ পাতালে প্রবেশ করে। তাই ভারতবর্ষ ইতিহাসের মহাশ্মশান নয়, মহাগোরস্থান। অতএব ভারতবর্ষের কবর খুঁড়ে তার ইতিহাস বার করতে হবে এই জ্ঞান হওয়ামাত্র আমাদের দেশের যত বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোকে কোদাল পাড়তে শর করলেন এই আশায় যে, এদেশের উত্তরে দক্ষিণে পূর্বে পশ্চিমে, যেখানেই কোদাল মারা যাবে সেখানেই, লস্তসভ্যতার গুপ্তধন বেরিয়ে পড়বে। আর সে ধনে আমরা এমনি ধনী হয়ে উঠব যে, মনোজগতে খোরপোশের জন্য আমাদের আর চাষ-আবাদ করতে হবে না।
এই খোঁড়াখুঁড়ির ফলে, সোনা না হোক তামা বেরিয়েছে, হীরে না থাক পাথর বেরিয়েছে। কিন্তু এ যে-সে তামা যে-সে পাথর নয়— সব হরফ-কাটা। এইসব মদ্রাঙ্কিত তাম্রফলকের বিশেষ-কিছু, মূল্য নেই, তা পয়সারই মত শস্তা। একালেও আমরা শিল কুটি, কিন্তু সেই কোটা-শিল পড়া যায় না; কেননা, তার অক্ষর সব রেখাক্ষর। কিন্তু অতীতের এই ক্ষোদিত পাষাণের কথা স্বতন্ত্র। বিদ্যা বলেছিলেন–
‘শিলা জলে ভেসে যায়, বানরে সংগীত গায়,
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়’
কিন্তু আজকাল যদি কেউ বলেন যে–
‘কপি জলে ভেসে যায়, পাষাণে সংগীত গায়,
দেখিলেও না হয় প্রত্যয়’
তাহলে তিনি অবিদ্যারই পরিচয় দেবেন। কেননা, আজকাল পাষাণের সংগীতে দেশ মাতিয়ে তুলেছে। অতীত আজ তার পাষাণ-বদনে তারস্বরে আত্মপরিচয় দিচ্ছে। কাগজের কথায় আমরা আর কান দিই নে। রামায়ণমহাভারত এখন উপন্যাস হয়ে পড়েছে, এবং ইতিহাস এখন বন্ধের শরণ গ্রহণ করেছে। তার কারণ, আমরা মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করেছি যে, যাকে আমরা হিসভ্যতা বলি সেটি একটি অর্বাচীন পদার্থ বৌদ্ধসভ্যতার পাকা বনিয়াদের উপরেই তা প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষের ইতিহাসের সর্বনিম্নস্তরে যা পাওয়া যায়, সে হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম। ফলে, আমরা হিন্দু হলেও বৌদ্ধধর্ম নিয়েই গৌরব করছিলাম। তাই প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, পাটলিপুত্রই হচ্ছে আমাদের ইতিহাসের কেন্দ্রস্থল একাধারে জন্মভূমি এবং পীঠস্থান।
৬.
কথাসরিৎসাগরের প্রসাদে পাটলিপুত্রের জন্মকথা আমরা সকলেই জানতুম। এবং আমরা, কাব্যরসের রসিকেরা, সেই জন্মবত্তান্তই সাদরে গ্রাহ্য করে নিয়েছিলুম; কেননা, সেকথায় বস্তুতন্ত্রতা না থাকলেও রস আছে, তাও আবার একটি নয়, তিন-তিনটি–মধুর বীর এবং অদ্ভুত রস। পত্রকর্তৃক পাটলিহরণের বত্তান্ত, কৃষ্ণকর্তৃক রক্মিণীহরণ এবং অর্জনকর্তৃক সুভদ্রাহরণের চাইতেও অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। কৃষ্ণ প্রভৃতি রথে চড়ে স্থূলপথে পলায়ন করেছিলেন, কিন্তু পত্র পাটলিকে ক্রোড়স্থ ক’রে মায়া-পাকায় ভর দিয়ে নভেমার্গে উড্ডীন হয়েছিলেন। কৃষ্ণার্জন স্ব স্ব নগরীতে প্রস্থান করেছিলেন; পত্র কিন্তু তাঁর মায়া-যঠির সাহায্যে যে-পরী আকাশে নির্মাণ করেছিলেন সেই পুরী ভূমিষ্ঠ হয়ে পাটলিপুত্র নাম ধারণ করে। বৈজ্ঞানিকেরা কিন্তু যাদতে বিশ্বাস করেন না। সুতরাং বৈজ্ঞানিক মতে পাটলিপুত্রকে খনন করা অবশ্যকর্তব্য হয়ে পড়েছিল, এবং সে কর্তব্যও সম্প্রতি কার্যে পরিণত করা হয়েছে। খোঁড়া-জিনিসটের ভিতর একটা বিপদ আছে, কেননা, কোনো-কোনো স্থলে কেঁচো খুড়তে সাপ বেরোয়। এক্ষেত্রে হয়েছেও তাই।
ডক্টর স্পূনার নামক জনৈক প্রত্নতত্ত্বের কর্তাব্যক্তি এই ভূমধ্য-রাজধানী খনন করে আবিষ্কার করেছেন যে, এদেশের মাটি খুড়লে দেখা যায় যে তার নীচে ভারতবর্ষ নেই, আছে শুধু পারশ্য। Palimpsest-নামক একপ্রকার প্রাচীন পথি পাওয়া যায়, যার উপরে এক ভাষায় লেখা থাকে আর নীচে আরএক ভাষায়। বলা বাহুল্য, উপরে যা লেখা থাকে তা জাল, আর নীচে যা লেখা থাকে তাই আসল। ডক্টর স্পূনারের দিব্যদৃষ্টিতে এতকাল পরে ধরা পড়েছে যে, আমরা যাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলি, সে হচ্ছে একটি বিরাট palimpsest; তার উপরে পালি কিংবা সংস্কৃতভাষায় যা লেখা আছে তা জাল, আর তার নীচে যা লেখা আছে তাই আসল। সে লেখা অবশ্য ফারসি; কেননা, আমরা কেউ তা পড়তে পারি নে। ডক্টর স্পূনারের কথা বৈজ্ঞানিকেরা মেনে না নিন, মান্য করতে বাধ্য; কেননা, সেকালের কাব্যের যাদুঘর হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু একালের যাদুঘরের কাব্যকে তা করা চলে না।
ডক্টর স্পূনার তাঁর নব-মত প্রতিষ্ঠা করবার জন্য নানা প্রমাণ, নানা অনুমান, নানা দর্শন, নানা নিদর্শন সংগ্রহ করেছেন। এসকলের মূল্য যে কি, তা নির্ণয় করা আমার সাধ্যের অতীত। এই পর্যন্ত বলতে পারি যে, তিনি এমন-একটি যুক্তি বাদ দিয়েছেন, যার আর কোনো খণ্ডন নেই। স্পূনার সাহেবের মতে যার নাম অসর তারই নাম দানব, এবং যার নাম দানব তারই নাম শক, এবং যার নাম শক তারই নাম পার্শি। একথা যদি সত্য হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, এদেশের মাটি খুঁড়লে পাশি-শহর বেরিয়ে পড়তে বাধ্য। দানবপরী যে পাতালে অর্থাৎ মাটির নীচে অবস্থিত, একথা তো হিন্দুর সর্বশাস্ত্রসম্মত।
৭.
অতএব দাঁড়াল এই যে, আমাদের ভবিষ্যৎও নেই অতীতও নেই। এক বাকি থাকল বর্তমান। সুতরাং বঙ্গসাহিত্যকে এখন থেকে এই বর্তমান নিয়েই কারবার করতে হবে। এ অবশ্য মহা মুশকিলের কথা। বই পড়ে বই লেখা এক, আর নিজে বিশ্বসংসার দেখেশুনে লেখা আর। একাজ করতে হলে চোখকান খুলে রাখতে হবে, মনকে খাটাতে হবে; এককথায় সচেতন হতে হবে। তার পর এত কষ্ট স্বীকার করে যে সাহিত্য গড়তে হবে, সে সাহিত্য সকলে সহজে গ্রাহ্য করবেন না। মানুষে বর্তমানকেই সবচাইতে অগ্রাহ্য করে। যাঁদের চোখকান বোজা আর মন পঙ্গু, তাঁরা এই নবসাহিত্যকে নবীন বলে নিন্দা করবেন। তবে এর মধ্যে আরামের কথা এই যে, বর্তমানের কোনো ইতিহাস নেই, সুতরাং এখন হতে বঙ্গসরস্বতীর ঘাড় থেকে ভূত নেমে যাবে।
আষাঢ় ১৩২৩
বর্ষার কথা
আমি যদি কবি হতুম, তাহলে আর যে বিষয়েই হোক, বর্ষার সম্বন্ধে কখনো কবিতা লিখতুম না। কেন? তার কারণগুলি ক্রমান্বয়ে উল্লেখ করছি।
প্রথমত, কবিতা হচ্ছে আট। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মতে আট-জিনিসটি দেশকালের বহিভূত। এ মতের সার্থকতা তাঁরা উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ করতে চান। হ্যামলেট, তাঁদের মতে, কালেতে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে না, এবং তার জন্মস্থানেও তাকে আবদ্ধ করে রাখবার জো নেই। কিন্তু সংগীতের উদাহরণ থেকে দেখানো যেতে পারে যে, এদেশে আর্ট কালের সম্পূর্ণ অধীন। প্রতি রাগরাগিণীর ক্ষতির ঋতু মাস দিন ক্ষণ নির্দিষ্ট আছে। যাঁর সুরের দৌড় শুধু ঋষভ পর্যন্ত পৌঁছয়, তিনিও জানেন যে, ভৈরবীর সময় হচ্ছে সকাল আর পুরবীর বিকাল। যেহেতু কবিতা গান থেকেই উৎপন্ন হয়েছে, সে কারণ সাহিত্যে সময়োচিত কবিতা লেখবারও ব্যবস্থা আছে। মাসিকপত্রে পয়লা বৈশাখে নববর্ষের কবিতা, পয়লা আষাঢ়ে বর্ষার, পয়লা আশ্বিনে পূজার, আর পয়লা ফাঙ্গনে প্রেমের কবিতা বেরনো চাইই চাই। এই কারণে আমার পক্ষে বর্ষার কবিতা লেখা অসম্ভব। যে কবিতা আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে প্রকাশিত হবে, তা অন্তত জ্যৈষ্ঠমাসের মাঝামাঝি রচনা করতে হবে। আমার মনের কল্পনার এত বাষ্প নেই যা নিদাঘের মধ্যাহ্নকে মেঘাচ্ছন্ন করে তুলতে পারে। তাছাড়া, যখন বাইরে অহরহ আগন জলছে তখন মনে বিরহের আগুন জালিয়ে রাখতে কালিদাসের যক্ষও সক্ষম হতেন কি না, সেবিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আর বিরহ বাদ দিয়ে বর্ষার কাব্য লেখাও যা, হ্যামলেটকে বাদ দিয়ে হ্যামলেটনাটক লেখাও তাই।
দ্বিতীয়ত, বর্ষার কবিতা লিখতে আমার ভরসা হয় না এই কারণে যে, এক ভরসা ছাড়া বরষা আর কোনো শব্দের সঙ্গে মেলে না। বাংলা-কবিতায় মিল চাই, এ ধারণা আমার আজও যে আছে, একথা আমি অস্বীকার করতে পারি নে। যখন ভাবের সঙ্গে ভাব না মিললে কবিতা হয় না, তখন কথার সঙ্গে কথা মিললে কেন যে তা কবিতা না হয়ে পদ্য হবে, তা আমি বুঝতে পারি নে। তাছাড়া, বাস্তবজীবনে যখন আমাদের কোনো কথাই মেলে না, তখন অন্তত একটা জায়গা থাকা চাই যেখানে তা মিলবে, এবং সেদেশ হচ্ছে কল্পনার রাজ্য, অর্থাৎ কবিতার জন্মভূমি। আর-এক কথা, অমিত্রাক্ষরের কবিতা যদি শ্রাবণের নদীর মত দল ছাপিয়ে না বয়ে যায়, তাহলে তা নিতান্ত অচল হয়ে পড়ে। মিল অর্থাৎ অন্তঃ-অনুপ্রাস বাদ দিয়ে পদ্যকে হিল্লোলে ও কল্লোলে ভরপুর করে তুলতে হলে মধ্য-অনুপ্রাসের ঘনঘটা আবশ্যক। সে কবিতার সঙ্গে সততসঞ্চরমান নবজলধরপটলের সংযোগ করিয়ে দিতে হয়, এবং তার চলোর্মির গতি যাদঃপতিরোধ ব্যতীত অন্য কোনোরূপ রোধ মানে না। আমার সরস্বতী হচ্ছেন প্রাচীন সরস্বতী, শঙ্কা না হলেও ক্ষীণা; দামোদর নন যে, শব্দের বন্যায় বাংলার সকল ছাঁদবাঁধ ভেঙে বেরিয়ে যাবেন। অতএব মিলের অভাববশতই আমাকে ক্ষান্ত থাকতে হচ্ছে। অবশ্য দরশ পরশ সরস হরষ প্রভৃতি শব্দকে আকার দিয়ে বরষার সঙ্গে মেলানো যায়। কিন্তু সে কাজ রবীন্দ্রনাথ আগেই করে বসে আছেন। আমি যদি ঐসকল শব্দকে সাকার করে ব্যবহার করি, তাহলে আমার চুরিবিদ্যে ঐ আকারেই ধরা পড়ে যাবে।
ঐরূপ শব্দসমূহ আত্মসাৎ করা চৌর্যবৃত্তি কি না, সেবিষয়ে অবশ্য প্রচণ্ড মতভেদ আছে। নব্যকবিদের মতে, মাতৃভাষা যখন কারও পৈতৃকসম্পত্তি নয়, তখন তা নিজের কার্যোপযোগী করে ব্যবহার করবার সকলেরই সমান অধিকার আছে। ঈষৎ বদল-সদল করেছেন বলে রবীন্দ্রনাথ ওসব কথার আরকিছু, পেটেট নেন নি যে, আমরা তা ব্যবহার করলে চোর-দায়ে ধরা পড়ব বিশেষত যখন তাদের কোনো বদলি পাওয়া যায় না। যেকথা একবার ছাপা হয়ে গেছে, তাকে আর চাপা দিয়ে রাখবার জো নেই; সে যার-তার কবিতায় নিজেকে ব্যক্ত করবে। নব্যকবিদের আর-একটি কথা বলবার আছে, যা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সে হচ্ছে এই যে, রবীন্দ্রনাথ যদি অনেক কথা আগে না ব্যবহার করে ফেলতেন, তাহলে পরবর্তী কবিরা তা ব্যবহার করতেন। পরে জন্মগ্রহণ করার দরুন সে সুযোগ হারিয়েছি বলে আমাদের যে চুপ করে থাকতে হবে, সাহিত্যজগতের এমন-কোনো নিয়ম নেই। এ মত গ্রাহ্য করলেও বর্ষার বিষয়ে কবিতা লেখার আর-একটি বাধা আছে। কলম ধরলেই মনে হয়, মেঘের সম্বন্ধে লিখব আর কি ছাই?
বর্ষার রূপগুণ সম্বন্ধে যা-কিছু, বক্তব্য ছিল, তা কালিদাস সবই বলে গেছেন, বাকি যা ছিল তা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। এবিষয়ে একটি নূতন উপমা কিংবা নূতন অনুপ্রাস খুঁজে পাওয়া ভার। যদি বাদ দিয়ে বর্ষার নগ্নমতির বর্ণনা করতে উদ্যত হই, তাহলেও বড় সুবিধে করতে পারা যায় না। কারণ, বর্ষার রূপ কালো, রস জোলো, গন্ধ পঙ্কজের নয়— পঙ্কের, স্পর্শ ভিজে, এবং শব্দ বেজায়। সুতরাং যে বর্ষা আমাদের ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত, তার যথাযথ বর্ণনাতে বস্তুতন্ত্রতা থাকতে পারে কিন্তু কবিত্ব থাকবে কি না, তা বলা কঠিন।
কবিতার যা দূরকার এবং যা নিয়ে কবিতার কারবার, সেইসব আনুষঙ্গিক উপকরণও এ ঋতুতে বড়-একটা পাওয়া যায় না। এ ঋতু পাখি-ছুট। বর্ষায় কোকিল মৌন, কেননা দর বক্তা; চকোর আকাশদেশত্যাগী, আর চাতক ঢের হয়েছে বলে ফটিকজল শব্দ আর মুখে আনে না। যেসকল চরণ ও চঞ্চসার পাখি, যথা বক হাঁস সারস হাড়গিলে ইত্যাদি, এ ঋতুতে স্বেচ্ছামত জলে-স্থলে ও নভোমণ্ডলে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে, তাদের গঠন এতই অদ্ভুত এবং তাদের প্রকৃতি এতই তামসিক যে, তারা যে বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি সেবিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই। বস্তুতন্ত্রতার খাতিরে আমরা অনেক দূর অগ্রসর হতে রাজি আছি, কিন্তু বিশ্বামিত্রের জগৎ পর্যন্ত নয়। তারপর কাব্যের উপযোগী ফল ফল লতা পাতা গাছ বর্ষায় এতই দুর্লভ যে, মহাকবি কালিদাসও ব্যাঙের ছাতার বর্ণনা করতে বাধ্য হয়েছেন। সংস্কৃতভাষার ঐশ্বর্যের মধ্যে এ দৈন্য ধরা পড়ে না, তাই কালিদাসের কবিতা বেচে গেছে। বর্ষার দুটি নিজস্ব ফল হচ্ছে কদম আর কেয়া। অপূর্বতায় পল্পজগতে এ দুটির আর তুলনা নেই। অপরাপর সকল ফল অর্ধবিকশিত ও অর্ধনিমীলিত। রূপের যে অধপ্রকাশ ও অর্ধগোপনেই তার মোহিনীশক্তি নিহিত, এ সত্য স্বর্গের অপ্সরারা জানতেন। মনিঋষিদের তপোভঙ্গ করবার জন্য তাঁরা উক্ত উপায়ই অবলম্বন করতেন। কারণ ব্যক্ত-দ্বারা ইন্দ্রিয় এবং অব্যক্ত-দ্বারা কল্পনাকে অভিভূত না করতে পারলে দেহ ও মনের সমষ্টিকে সম্পূর্ণ মোহিত করা যায় না। কদম কিন্তু একেবারেই খোলা, আর কেয়া একেবারেই বোজা। একের ব্যক্ত-রপ নেই, অপরের গল্ড-গন্ধ নেই; অথচ উভয়েই কণ্টকিত। এ ফল দিয়ে কবিতা সাজানো যায় না। এ দুটি ফল বর্ষার ভূষণ নয়, অস্ব; গোলা এবং সঙিনের সঙ্গে এদের সাদশ্য স্পষ্ট।
পূর্বে যা দেখানো গেল, সেসব তো অঙ্গহীনতার পরিচয়। কিন্তু এ ঋতুর প্রধান দোষ হচ্ছে, আর-পাঁচটি ঋতুর সঙ্গে এর কোনো মিল নেই; আর-পাঁচটি ঋতুর সঙ্গে এ ঋতু খাপ খায় না। এ ঋতু বিজাতীয় এবং বিদেশী, অতএব অস্পশ্য। এই প্রক্ষিপ্ত ঋতু আকাশ থেকে পড়ে, দেশের মাটির ভিতর থেকে আবির্ভূত হয় না। বসন্তের নবীনতা সজীবতা ও সরসতার মূল হচ্ছে ধরণী। বসন্তের ঐশ্বর্য হচ্ছে দেশের ফলে, দেশের কিশলয়ে। বসন্তের দক্ষিণপবনের জন্মস্থান যে ভারতবর্ষের মলয়পর্বত, তার পরিচয় তার পশেই পাওয়া যায়; সে পবন আমাদের দেহে চন্দনের প্রলেপ দিয়ে দেয়। বসন্তের আলো, সূর্য ও চন্দ্রের আলো। ও দুটি দেবতা তো সম্পূর্ণ আমাদেরই আত্মীয়; কেননা, আমরা হয় সূর্যবংশীয় নয় চন্দ্রবংশীয় এবং ভবলীলাসংবরণ করে আমরা হয় সযলোকে নয় চন্দ্রলোকে ফিরে যাই। অপরপক্ষে, মেঘ যে কোন দেশ থেকে আসে, তার কোনো ঠিকানা নেই। বর্ষা যে-জল বর্ষণ করে, সে কালাপানির জল। বর্ষার হাওয়া এতই দুরন্ত এতই অশিষ্ট এতই প্রচণ্ড এবং এতই স্বাধীন যে, সে-যে কোনো অসভ্য দেশ থেকে আসে, সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তারপর, বর্ষার নিজস্ব আলো হচ্ছে বিদ্যৎ। বিদ্যতের আলো এতই হাস্যোজ্জল এতই চঞ্চল এতই বক্র এবং এতই তীক্ষন যে, এই প্রশান্ত মহাদেশের এই প্রশান্ত মহাকাশে সে কখনোই জন্মলাভ করে নি। আর-এক কথা, বসন্ত হচ্ছে কলকাঠ কোকিলের পঞ্চম সরে মুখরিত। আর বর্ষার নিনাদ? তা শুনে শুধু যে কানে হাত দিতে হয় তা নয়, চোখও বুজতে হয়।
বর্ষার প্রকৃতি যে আমাদের প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিপরীত, তার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় ও-ঋতুর ব্যবহারে। এ-ঋতু শুধু বেখাপা নয়, অতি বেআড়া। বসন্ত যখন আসে, সে এত অলক্ষিতভাবে আসে যে, পঞ্জিকার সাহায্য ব্যতীত কবে মাঘের শেষ হয় আর কবে ফাল্গুনের আরম্ভ হয়, তা কেউ বলতে পারেন না। বসন্ত, বঙ্কিমের রজনীর মত, ধীরে ধীরে অতিধীরে ফলের ডালা হাতে করে, দেশের হদয়-মন্দিরে এসে প্রবেশ করে। তার চরণস্পর্শে ধরণীর মুখে, শব-সাধকের শবের ন্যয়ি, প্রথমে বর্ণ দেখা দেয়, তার পরে ভ, কম্পিত হয়, তার পরে চক্ষু উন্মীলিত হয়, তার পর তার নিশ্বাস পড়ে, তার পর তার সর্বাঙ্গ শিহরিত হয়ে ওঠে। এসকল জীবনের লক্ষণ শুধু পর্যায়ক্রমে নয়, ধীরে ধীরে অতিধীরে প্রকটিত হয়। কিন্তু বর্ষা ভয়ংকর মতি ধারণ ক’রে একেবারে ঝাঁপিয়ে এসে পড়ে। আকাশে তার চুল ওড়ে, চোখে তার বিদ্যৎ খেলে, মুখে তার প্রচণ্ড হংকার; সে যেন একেবারে প্রমত্ত, উন্মত্ত। ইংরেজেরা বলেন, কে কার সঙ্গ রাখে, তার থেকে তার চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। বসন্তের সখা মদন। আর বর্ষার সখা? পবননন্দন নন, কিন্তু তাঁর বাবা। ইনি একলক্ষ্যে আমাদের অশোকবনে উত্তীর্ণ হয়ে ফল ছে’ড়েন, ডাল ভাঙেন, গাছ ওপড়ান; আমাদের সোনার লঙ্কা একদিনেই লণ্ডভণ্ড করে দেন, এবং যে সৰ্য আমাদের ঘরে বাঁধা রয়েছে তাকে বগলদাবা করেন; আর চন্দ্রের দেহ ভয়ে সংকুচিত হয়ে তার কলঙ্কের ভিতর প্রবিষ্ট হয়ে যায়। এককথায়, বর্ষার ধর্ম হচ্ছে জল-স্থল-আকাশ সব বিপর্যস্ত করে ফেলা। এ-ঋতু কেবল পৃথিবী নয়, দিবারাত্রেরও সাজানো তাস ভেস্তে দেয়। তাছাড়া বর্ষা কখনো হাসেন কখনো কাঁদেন, ইনি ক্ষণে রষ্ট ক্ষণে তুষ্ট। এমন অব্যবস্থিতচিত্ত ঋতুকে ছন্দোবন্ধের ভিতর সুব্যবস্থিত করা আমার সাধ্যাতীত।
এস্থলে এই আপত্তি উঠতে পারে যে, বর্ষার চরিত্র যদি এতই উদ্ভট হয়, তাহলে কালিদাস প্রভৃতি মহাকবিরা কেন ও-ঋতুকে তাঁদের কাব্যে অতখানি স্থান দিয়েছেন। তার উত্তর হচ্ছে যে, সেকালের বর্ষা আর একালের বর্ষা এক জিনিস নয়; নাম ছাড়া এ উভয়ের ভিতর আর-কোনো মিল নেই। মেঘদতের মেঘ শান্ত-দান্ত; সে বন্ধুর কথা শোনে, এবং যে পথে যেতে বলে, সেই পথে যায়। সে যে কতদূর রসজ্ঞ, তা তার উজ্জয়িনী-প্রয়াণ থেকেই জানা যায়। সে রমণীর হদয়জ্ঞ, প্রীজাতির নিকট কোন ক্ষেত্রে হংকার করতে হয় এবং কোন ক্ষেত্রে অল্পভাষে জল্পনা করতে হয়, তা তার বিলক্ষণ জানা আছে। সে করণ, সে কনকনিকষস্নিগ্ধ বিজলির বাতি জেলে সচিভেদ্য অন্ধকারের মধ্যে অভিসারিকাদের পথ দেখায়, কিন্তু তাদের গায়ে জল বর্ষণ করে না। সে সংগীতজ্ঞ, তার সখা অনিল যখন কীচক-রন্ধে মুখ দিয়ে বংশীবাদন করেন, তখন সে মদঙ্গের সংগত করে। এককথায় ধীরোদাত্ত নায়কের সকল গণই তাতে বর্তমান। সে মেঘ তো মেঘ নয়, পপকরথে আরঢ় স্বয়ং বরুণদেব। সে রথ অলকার প্রাসাদের মত ইন্দ্রচাপে সচিত্র, ললিতবনিতাসনাথ মরজনিতে মুখরিত। সে মেঘ কখনো শিলাবৃষ্টি করে না, মধ্যে মধ্যে পুষ্পবৃষ্টি করে। এহেন মেঘ যদি কবিতার বিষয় না হয়, তাহলে সে বিষয় আর কি হতে পারে?
কিন্তু যেহেতু আমাদের পরিচিত বর্ষা নিতান্ত উদভ্রান্ত উচ্ছখল, সেই কারণেই তার বিষয় কবিত্ব করা সম্ভব হলেও অনুচিত। পৃথিবীতে মানুষের সব কাজের ভিতর একটা উদ্দেশ্য আছে। আমার বিশ্বাস, প্রকৃতির রূপবর্ণনার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার সৌন্দর্যের সাহায্যে মানব-মনকে শিক্ষাদান করা। যদি তাই হয়, তাহলে কবিরা কি বর্ষার চরিত্রকে মানুষের মনের কাছে আদর্শস্বরূপ ধরে দিতে চান। আমাদের মত শান্ত সমাহিত সুসভ্য জাতির পক্ষে, বর্ষা নয়, হেমন্ত হচ্ছে আদর্শ ঋতু। এ মত আমার নয়, শাস্ত্রের’; নিম্নে উদ্ধত বাক্যগুলির দ্বারাই তা প্রমাণিত হবে :
‘ঋতুগণের মধ্যে হেমন্তই স্বাহাকার, কেননা হেমন্ত এই প্রজাসমূহকে নিজের বশীভূত করিয়া রাখে, এবং সেইজন্য হেমতে ওষধিসমূহ ম্লান হয়, বনস্পতিসমূহের পত্রনিচয় নিপতিত হয়, পক্ষীসমূহ যেন অধিকতরভাবে স্থির হইয়া থাকে ও অধিকতর নীচে উড়িয়া বেড়ায়, এবং নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের লোমসমূহ যেন (শীতপ্রভাবে) নিপতিত হইয়া যায়, কেননা হেমন্ত এইসমস্ত প্রজাকে নিজের বশীভূত করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি ইহা এইরূপ জানেন, তিনি যে (ভূমি) ভাগে থাকেন তাহাকেই শ্রী ও শ্রেষ্ঠ অন্নের জন্য নিজের করিয়া তোলেন।’— শতপথ ব্রাহরণ।
আমরা যে শ্রীভ্রষ্ট এবং শ্রেষ্ঠ-অন্নহীন, তার কারণ আমরা হেমন্তকে এইরূপে জানি নে; এবং জানি নে যে, তার কারণ, কবিরা হেমন্তের স্বরূপের বর্ণনা করেন না, বর্ণনা করেন শুধু বর্ষার; যে বর্ষা ওষধিসমূহকে ম্লান না করে সবুজ করে তোলে।
আষাঢ় ১৩২১
বীরবলের চিঠি
মহারাজা শ্রীযুক্ত জগদিন্দ্রনাথ রায়,
‘মানসী’সম্পাদকমহাশয় করকমলেষু
মানসী যে সম্পাদকসঙেঘর হাত থেকে উদ্ধারলাভ করে অতঃপর রাজআশ্রয় গ্রহণ করেছে, এতে আমি খুশি; কেননা, এদেশে পরাকালে কি হত তা পুরাতত্ত্ববিদেরা বলতে পারেন কিন্তু একালে যে সব জিনিসই পঞ্চায়তের হাতে পঞ্চত্ব লাভ করে, সেবিষয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই।
আমার খুশি হবার একটি বিশেষ কারণ এই যে আমার জন্য মানসী যা করেছেন, অন্য কোনো পত্রিকা তা করেন নি। অপরে আমার লেখা ছাপান, মানসী আমার ছবিও ছাপিয়েছেন। লেখা নিজে লিখতে হয়, ছবি অন্যে তুলে নেয়। প্রথমটির জন্য নিজের পরিশ্রম চাই, ছবি সম্বন্ধে কষ্ট অপরের— যিনি আঁকেন ও যিনি দেখেন।
তাই আপনি মানসীর সম্পাদকীয় ভার নেওয়াতে আমি ষোলোআনা খুশি হতুম, যদি আপনি ছাপাবার জন্য আমার কাছে লেখা না চেয়ে আলেখ্য চাইতেন। এর কারণ পূর্বেই উল্লেখ করেছি। রাজাজ্ঞা সবথা শিরোধার্য হলেও সর্বদা পালন করা সম্ভব নয়। রাজার আদেশে মুখ বন্ধ করা সহজ, খোলা কঠিন। পৃথিবীতে সাহিত্য কেন, সকল ক্ষেত্রেই নিষেধ মান্য করা বিধি অনুসরণ করার চাইতে অনেক সহজসাধ্য। এর ওর হাতে জল খেয়ো না’–এই নিষেধ প্রতিপালন করেই ব্রাহ্মণজাতি আজও টিকে আছেন, বেদ-অধ্যয়নের বিধি পালন করতে বাধ্য হলে কবে মারা যেতেন।
সে যাই হোক, একথা সত্য যে, আমার মত লেখকের সাহায্যে সাহিত্যজগতের কোনো কাজ কিংবা কাগজসম্পাদন করা যায় না; কেননা, আমি সরস্বতীর মন্দিরের পূজারী নই, স্বেচ্ছাসেবক। স্বেচ্ছাসেবার যতই কেন গুণ থাকুক না, তার মহাদোষ এই যে, সে-সেবার উপর বারোমাস নির্ভর করা চলে না। আর মাসিকপত্রিকা নামে মাসিক হলেও, আসলে বারোমেসে। তাছাড়া পত্রের প্রত্যাশায় কেউ শিমুলগাছের কাছে ঘেঁষে না; এবং আমি যে সাহিত্যউদ্যানের একটি শাল্মলীতর, তার প্রমাণ আমার গদ্যপদ্যেই পাওয়া যায়। লোকে বলে, আমার লেখার গায়ে কাঁটা, আর মাথায় মধুহীন গন্ধহীন ফল।
আর-একটি কথা। সম্প্রতি কোনো বিশেষ কারণে প্রতিদিন আমার কাছে শ্রীপঞ্চমী হয়ে উঠেছে; মনে হয় কলম না ছোঁয়াটাই সরস্বতীপুজোর প্রকৃষ্ট উপায়। এর কারণ নিম্নে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করছি।
আপনি জানেন যে, লেখকমাত্রেরই একটি বিশেষ ধরন আছে, সেই নিজস্ব : ধরনে রচনা করাই তার পক্ষে স্বাভাবিক এবং কর্তব্য। পরের ঢঙের নকল করে শুধু সং। যা লিখতে আমি আনন্দ লাভ করি নে, তা পড়তে যে পাঠকে আনন্দ লাভ করবেন, যে লেখায় আমার শিক্ষা নেই, সে লেখায় যে পাঠকের শিক্ষা হবে, এত বড় মিথ্যা কথাতে আমি বিশ্বাস করি নে। আমার দেহমনের ভগিটি আমার চিরসঙগী, সেটিকে ত্যাগ করা অসম্ভব বললেও অত্যুক্তি হবে না। সমালোচকদের তাড়নায় লেখার ভঙ্গিটি ছাড়ার চাইতে লেখা ছাড়া ঢের সহজ; অথচ সমালোচকদের মনোরঞ্জন করতে হলে হয়ত আমার লেখার ঢং বদলাতে হবে।
আমার কলমের মুখে অক্ষরগুলো সহজেই একটু বাঁকা হয়ে বেরোয়। আমি সেগুলি সিধে করতে চেষ্টা না করে যেদিকে তাদের সহজ গতি সেইদিকেই ঝোঁক দিই। কিন্তু এর দরুন আমার লেখা যে এত বঙ্কিম হয়ে উঠেছে যে, তা ফারসি বলে কারও ভ্রম হতে পারে–এ সন্দেহ আমার মনে কখনো উদয় হয় নি। অথচ আমার বাংলা যে কারও-কারও কাছে ফারসি কিংবা আরবি হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ মানসীতেই পাওয়া যায়। আমি ননাবেল প্রাইজ নিয়ে যে একটু রসিকতা করবার প্রয়াস পেয়েছিলুম, মানসীর সমালোচক তা তত্ত্বকথাহিসাবে অগ্রাহ্য করেছেন। যদি কেউ রসিকতাকে রসিকতা বলে না বোঝেন, তাহলে আমি নিরপায়; কারণ তর্ক করে তা বাঝানো যায় না। যেকথা একবার জমিয়ে বলা গেছে, তার আর ফেনিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে না।
এ অবস্থায় যদি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে, আমার কপালে অরসিকে রসনিবেদন ‘মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ’, তাহলে সমালোচকেরাও আমাকে বলবেন, ‘মা লিখ, মা লিখ, মা লিখ’। এদের উপদেশ অনুসারে রসিকতা করার অভ্যাসটা ত্যাগ করতে রাজি আছি, যদি কেউ আমাকে এ ভরসা দিতে পারেন যে, সত্যকথা বললে এরা তা রসিকতা মনে করবেন না। সে ভরসা কি আপনি দিতে পারেন?
লোকে বলে সাহিত্যের উদ্দেশ্য, হয় লোকের মনোরঞ্জন করা, নয় শিক্ষা দেওয়া। আমার বিশ্বাস সাহিত্যের উদ্দেশ্য দুই নয়, এক। এক্ষেত্রে উপায়ে ও উদ্দেশ্যে কোনো প্রভেদ নেই। এই শিক্ষার কথাটাই ধরা যাক। সাহিত্যের শিক্ষা ও স্কুলের শিক্ষা এক নয়। সাহিত্যে লেখক ও পাঠকের সম্বন্ধ গুরশিষ্যের সম্বন্ধ নয়, বয়স্যের সম্বন্ধ। সুতরাং সাহিত্যে নিরানন্দ শিক্ষার স্থান নেই। অপরদিকে, যেকথার ভিতর সত্য নেই, তা ছেলের মন ভোলাতে পারে কিন্তু মানুষের মনোরঞ্জন করতে পারে না।
রহস্য করে যাদের মনোরঞ্জন করতে পারলম না, স্পষ্ট কথা বলে যে তাঁদের মনোরঞ্জন করতে পারব— এ হচ্ছে আশা ছেড়ে আশা রাখা। আর, কথায় যদি মানুষের মনই না পাওয়া যায়, তাহলে সেকথা বিড়ম্বনা মাত্র। ভয় তো ঐখানেই।
সত্যকথা সুস্থ মনের পক্ষে আহার রুচিকরও বটে, পুষ্টিকরও বটে, কিন্তু রুগ্ণ মনের পক্ষে তা ঔষধ, তাতে উপকার যা তা পরে হবে— পেটে গেলে, তাও আবার যদি লাগে; কিন্তু গলাধঃকরণ করবার সময় তা কটুকষায়। বাংলার মনোরাজ্যেও ম্যালেরিয়া যে মোটেই নেই, এরূপ আমার ধারণা নয়। সুতরাং শাদাভাবে সিধে কথা বলতে আমি ভয় পাই।
রসিকতা ছাড়লে আমাকে চিন্তাশীল’ লেখক হতে হবে অর্থাৎ অতি গম্ভীরভাবে অতি সাধভাষায় বারবার হয়কে নয় এবং নয়কে হয় বলতে হবে। কারণ, যা প্রত্যক্ষ তাকেই যদি সত্য বলি, তাহলে আর গবেষণার কি পরিচয় দিলম। কিন্তু আমার পক্ষে ওরূপ করা সহজ নয়। ভগবান, আমার বিশ্বাস, মানুষকে চোখ দিয়েছেন চেয়ে দেখবার জন্য–তাতে ঠলি পরবার জন্য নয়। সে ঠলির বাম দর্শন দিলেও তা অগ্রাহ্য। শুনতে পাই, চোখে ঠলি না দিলে গোরতে ঘানি ঘোরায় না। একথা যদি সত্য হয়, তাহলে যাঁরা সংসারের ঘানি ঘোরাবার জন্য ব্যত, লেখকেরা তাঁদের জন্য সাহিত্যের ঠলি প্রস্তুত করতে পারেন, কিন্তু আমি তা পারব না। কেননা, আমি ও ঘানিতে নিজেকেও জতে দিতে চাই নে, তাপর কাউকেও নয়। আমি চাই অপরের চোখের সে ঠলি খুলে দিতে; শুধু শিং-বাঁকানোর ভয়ে নিরস্ত হই। ফলে দাঁড়াল এই যে, রসিকতা করা নিরাপদ নয়, আর সত্য কথা বলাতে বিপদ আছে।
দুটি-একটি উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন যে, আমি ঠিক কথা বলছি। বাঙালি যুবকের পক্ষে সমুদ্রযাত্রার পথে প্রতিবন্ধক যে ধর্ম নয় কিন্তু অর্থ, এ প্রত্যক্ষ সত্য; কারণ তাঁদের কাছে ধর্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত, এবং অর্ণবযানেরা যে পথে যাতায়াত করে স এব পন্থা। অথচ এইকথা বলতে গেলে সমগ্র ব্রাহ্মণ-মহাসভা এসে আমার স্কন্ধে ভর করবেন।
স্নেহলতা যে-চিতায় নিজের দেহ ভস্মসাৎ করেছেন, সে-চিতার আগুনের আঁচ যে সমগ্র সমাজের গায়ে অল্পবিস্তর লেগেছে, সেবিষয়ে আর সন্দেহ নেই। কারণ কুমারীদাহ-ব্যাপারটি এদেশে নতুন, ও উপলক্ষ্যে এখনো আমরা ঢাকঢোল বাজাতে শিখি নি। কিন্তু তাই বলে যাঁদের দেখা যাচ্ছে অত্যন্ত গাত্রজালা হয়েছে, তাঁরাও যে সেই চিতাভস্ম গায়ে মেখে বিবাগী হয়ে যাবেন, এরূপ বিশ্বাস আমার নয়। যে আগুন আজ সমাজের মনে জলে উঠেছে, সে হচ্ছে খড়ের আগুন দপ করে জলে উঠে আবার অমনি নিভে যাবে। আজ ঝোঁকের মাথায় মনে-মনে যিনি যতই কঠিন পণ করুন না কেন, তার একটিও টিকবে না— থাকবে শুধু বরপণ। যতদিন সমাজ বাল্যবিবাহকে বৈধ এবং অসবর্ণ-বিবাহকে নিষিদ্ধ বলে মেনে নেবেন, ততদিন মানুষকে বাধ্য হয়ে বরপণ দিতেও হবে এবং নিতেও হবে। বিবাহাদি সম্বন্ধে অত সংকীর্ণ জাতিধর্ম রাখতে হলে ব্যক্তিগত অর্থ থাকা চাই। এ সত্য অঙ্ক কষে প্রমাণ করা যায়। মূলকথা এই যে, সনাতন প্রথা বর্তমানে সংসারযাত্রার পক্ষে অচল। এবং অচলের চলন করতে গিয়েই আমাদের দুর্গতি। কিন্তু এইকথা বললে সমাজ হয়ত আমার জন্য তুষানলের ব্যবস্থা করবেন।
মোদ্দাকথা এই যে, বাজেকথা শুনলে লোকে মুখ অন্ধকার করে, এবং কাজের কথা শুনলে চোখ লাল করে। এ অবস্থায় ‘বোবার শত্র, নেই’ এই শাস্ত্রবচন অনুসারে চুপ করে থাকাই শ্রেয়। সম্ভবত ভারতবর্ষে পুরাকালের অবস্থা এই একই রকমেরই ছিল, এবং সেইজন্যই সেকালে জ্ঞানীরা মনি হতেন।
বৈশাখ ১৩২১
মলাট-সমালোচনা
‘সাহিত্য’সম্পাদকমহাশয় সমীপেষু
‘বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি’ -জিনিসটা এদেশে একটা মস্ত ঠাট্টার সামগ্রী। কিন্তু বারো পাতা বইয়ের তেরো পাতা সমালোচনা দেখে কারোই হাসি পায় না। অথচ বীজ পরিমাণে এক হাত কমই হোক আর এক হাত বেশিই হোক, তার থেকে নতুন ফল জন্মায়; কিন্তু ঐরূপ সমালোচনায় সাহিত্যের কিংবা সমাজের কি ফললাভ হয়, বলা কঠিন। সেকালে যখন সত্রআকারে মূল গ্রন্থ রচনা করবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল, তখন ভাষ্যে-টীকায়কারিকায় তার বিস্তৃত ব্যাখ্যার আবশ্যকতা ছিল। কিন্তু একালে যখন, যেকথা দু কথায় বলা যায় তাই দ শ কথায় লেখা হয়, তখন সমালোচকদের ভাষ্যকার না হয়ে সত্ৰকার হওয়াই সংগত। তাঁরা যদি কোনো নব্যগ্রন্থের খেই ধরিয়ে দেন, তাহলেই আমরা পাঠকবর্গ যথেষ্ট মনে করি। কিন্তু ঐরূপ করতে গেলে তাঁদের ব্যাবসা মারা যায়। সুতরাং তাঁরা যে সমালোচনার রীতিপরিবর্তন করবেন, এরূপ আশা করা নিষ্ফল।
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অত্যুক্তির প্রতিবাদ করে একটি প্রবন্ধ লেখেন। আমার ঠিক মনে নেই যে, তিনি সাহিত্যেও অত্যুক্তি যে নিন্দনীয়, একথাটা বলেছেন কি না। সে যাই হোক, রবীন্দ্রবাবুর সেই তীব্র প্রতিবাদে বিশেষ কোনো সুফল হয়েছে বলে মনে হয় না। বরং দেখতে পাই যে, অত্যুক্তির মাত্রা ক্রমে সপ্তমে চড়ে গেছে। সমালোচকদের অত্যুক্তিটা প্রায় প্রশংসা করবার সময়েই দেখা যায়। বোধ হয় তাঁদের বিশ্বাস যে, নিন্দা-জিনিসটা সোজা কথাতেই করা চলে কিন্তু প্রশংসাকে ডালপালা দিয়ে পত্রে-পুষ্পে সাজিয়ে বার করা উচিত। কেননা, নিন্দুকের চাইতে সমাজে চাটকারের মর্যাদা অনেক বেশি। কিন্তু আসলে অতিনিন্দা এবং অতিপ্রশংসা উভয়ই সমান জঘন্য। কারণ, অত্যুক্তির ‘অতি’ শুধু সুরুচি এবং ভদ্রতা নয়, সত্যেরও সীমা অতিক্রম করে যায়। এককথায়, অত্যুক্তি মিথ্যোক্তি। মিছাকথা মানযে বিনা কারণে বলে না। হয় ভয়ে নাহয় কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্যই লোকে সত্যের অপলাপ করে। সম্ভবত অভ্যাসবশত মিথ্যাকে সত্যের অপেক্ষা অধিকমাত্রায় কেউ-কেউ চর্চা করে। কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে মিথ্যাকথা বলা চর্চা করলে ক্রমে তা উদ্দেশ্যবিহীন অভ্যাসে পরিণত হয়। বাংলাসাহিত্যে আজকাল যেরূপ নির্লজ্জ অতিপ্রশংসার বাড়াবাড়ি দেখতে পাওয়া যায়, তাতে মনে হয় যে, তার মূলে উদ্দেশ্য এবং অভ্যাস দুই জিনিসই আছে। এক-একটি ক্ষুদ্র লেখকের ক্ষুদ্র পস্তকের যেসকল বিশেষণে স্তুতিবাদ করা হয়ে থাকে, সেগুলি বোধ হয় শেক্সপীয়র কিংবা কালিদাসের সম্বন্ধে প্রয়োগ করলেও একটু বেশি হয়ে পড়ে। সমালোচনা এখন বিজ্ঞাপনের মতি ধারণ করেছে। তার থেকে বোঝা যায় যে, যাতে বাজারে বইয়ের ভালোরকম কাটতি হয়, সেই উদ্দেশ্যে আজকাল সমালোচনা লেখা হয়ে থাকে। যে উপায়ে পেটেন্ট ঔষধ বিক্রি করা হয়, সেই উপায়েই সাহিত্যও বাজারে বিক্রি করা হয়। লেখক সমালোচক হয় একই ব্যক্তি, নয় পরপরে একই কারবারের অংশীদার। আমার মাল তুমি যাচাই করে পয়লা নম্বরের বলে দাও, তোমার মাল আমি যাচাই করে পয়লা নম্বরের বলে দেব, এইরকম একটা বন্দোবস্ত পেশাদার লেখকদের মধ্যে যে আছে, একথা সহজেই মনে উদয় হয়। এই কারণেই, পেটেন্ট ঔষধের মতই একালের ছোটগল্প কিংবা ছোটকবিতার বই মেধা হ্রী ধী শ্রী প্রভৃতির বর্ধক এবং নৈতিক-বলকারক বলে উল্লিখিত হয়ে থাকে। কিন্তু এরূপ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে পাঠক নিত্যই প্রতারিত এবং প্রবঞ্চিত হয়। যা চ্যবনপ্রাশ বলে কিনে আনা হয় তা দেখা যায় প্রায়ই অকালকুষ্মাণ্ডখণ্ডমাত্র।
অতি-বিজ্ঞাপিত জিনিসের প্রতি আমার শ্রদ্ধা অতি ম। কারণ, মানবহাদয়ের স্বাভাবিক দুর্বলতার উপর বিজ্ঞাপনের হল, এবং মানবমনের সরল বিশ্বাসের উপর বিজ্ঞাপনের ছল প্রতিষ্ঠিত। যখন আমাদের একমাথা চুল থাকে, তখন আমরা কেশবধক তৈলের বড়-একটা সন্ধান রাখি নে। কিন্তু মাথায় যখন টাক চকচক করে ওঠে, তখনই আমরা কুতলবষ্যের শরণ গ্রহণ করে নিজেদের অবিমৃষ্যকারিতার পরিচয় পাই এবং দিই। কারণ, তাতে টাকের প্রসার ক্রমশই বৃদ্ধি পায়, এবং সেইসঙ্গে টাকাও নষ্ট হয়। বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য আমাদের মন ও নয়ন আকর্ষণ করা। বিজ্ঞাপন প্রতি ছত্রের শেষে প্রশ্ন করে— মনোযোগ করছেন তো?’ আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করতে না পারলেও, বিজ্ঞাপন চব্বিশঘণ্টা আমাদের নয়ন আকর্ষণ করে থাকে। ও জিনিস চোখ এড়িয়ে যাবার জো নেই। কারণ, এ যুগে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রবন্ধের গা ঘেঁষে থাকে, মাসিকপত্রিকার শিরোভূষণ হয়ে দেখা দেয়; এককথায় সাহিত্যজগতে যেখানেই একটু ফাঁক দেখে, সেইখানেই এসে জুড়ে বসে। ইংরেজিভাষায় একটি প্রবচন আছে যে, প্রাচীরের কান আছে। এদেশে সে বধির কি না জানি নে, কিন্তু বিজ্ঞাপনের দৌলতে মক নয়। রাজপথের উভয় পার্শ্বের প্রাচীর মিথ্যাকথা তারস্বরে চীৎকার করে বলে। তাই আজকাল পৃথিবীতে চোখকান না বুজে চললে বিজ্ঞাপন কারও ইন্দ্রিয়ের অগোচর থাকে না। যদি চোখকান বুজে চল, তাহলেও বিজ্ঞাপনের হাত থেকে নিস্তার নেই। কারণ, পদব্রজেই চল, আর গাড়িতেই যাও, রাস্তার লোকে তোমাকে বিজ্ঞাপন ছড়ে মারে। এতে আশ্চর্য হবার কোনো কথা নেই; ছুড়ে মারাই বিজ্ঞাপনের ধর্ম। তার রং ছড়ে মারে, তার ভাষা ছড়ে মারে, তার ভাব ছুড়ে মারে। সুতরাং বিজ্ঞাপিত জিনিসের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা না থাকলেও তার মোড়কের সঙ্গে এবং মলাটের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় আছে। আমি বহু ঔষধের এবং বহু গ্রন্থের কেবলমাত্র মুখ চিনি ও নাম জানি। যা জানি, তারই সমালোচনা করা সম্ভব। সুতরাং আমি মলাটের সমালোচনা করতে উদ্যত হয়েছি। অন্তত মুখপাতটকু দোরস্ত করে দিতে পারলে আপাতত বঙ্গসাহিত্যের মুখরক্ষা হয়।
আমি পূর্বেই বলেছি যে, নব্য বঙ্গসাহিত্যের কেবলমাত্র নাম-রূপের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। প্রধানত সেই নাম-জিনিসটার সমালোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু রূপ-জিনিসটে একেবারে ছেটে দেওয়া চলে না বলে সেসম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলতে চাই। ডাক্তারখানার আলো যেমন লাল নীল সবুজ বেগনে প্রভৃতি নানারূপ কাঁচের আবরণের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়, তেমনি পুস্তকের দোকানে একালের পুস্তক-পুস্তিকাগুলি নানারূপ বর্ণচ্ছটায় নিজেদের প্রকাশ করে। সুতরাং নব্যসাহিত্যের বর্ণপরিচয় যে আমার হয় নি, একথা বলতে পারি নে। কবিতা আজকাল গোধুলিতে গা-ঢাকা দিয়ে ‘লজ্জান নববধ সম’ আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয় না; কিন্তু গালে আলতা মেখে রাজপথের সম্মুখে বাতায়নে এসে দেখা দেয়। বর্ণেরও একটা আভিজাত্য আছে। তার সসংযত ভাবের উপরেই তার গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য নির্ভর করে। বাড়াবাড়ি-জিনিসটা সব ক্ষেত্রেই ইতরতার পরিচায়ক। আমার মতে পুজার বাজারের নানারূপ রংচঙে পোশাক পরে প্রাপ্তবয়স্ক সাহিত্যের সমাজে বার হওয়া উচিত নয়। তবে পুজার উপহারস্বরূপে যদি তার চলন হয়, তাহলে অবশ্য কিছু বলা চলে না। সাহিত্য যখন কুন্তলীন তাম্বুলীন এবং তরলআলতার সঙ্গে একশ্রেণীভুক্ত হয়, তখন পুরুষের পক্ষে পুরুষ বাক্য ছাড়া তার সম্বন্ধে অন্যকোনো ভাষা ব্যবহার করা চলে না। তবে এইকথা জিজ্ঞাসা করি যে, এতে যে আত্মমর্যাদার লাঘব হয়, এ সহজ কথাটা কি গ্রন্থকারেরা বুঝতে পারেন না; কবি কি চান যে, তাঁর হদয়রক্ত তরল-আল তার শামিল হয়; চিন্তাশীল লেখক কি এইকথা মনে করে সুখী হন যে, তাঁর মস্তিষ্ক লোকে সুবাসিত নারিকেলতৈল হিসাবে দেখবে; এবং বাণী কি রসনানিঃসত পানের পিকের সঙ্গে জড়িত হতে লজ্জা বোধ করেন না? আশা করি যে, বইয়ের মলাটের এই অতিরঞ্জিত রূপ শীঘ্রই সকলের পক্ষেই অরুচিকর হয়ে উঠবে। অ্যান্টিক কাগজে ছাপানো এবং চকচকে ঝকঝকে তর্কতকে করে বাঁধানো পুস্তকে আমার কোনো আপত্তি নেই। দপ্তরিকে আসল গ্রন্থকার বলে ভুল না করলেই খুশি হই। আমরা যেন ভুলে না যাই যে, লেখকের কৃতিত্ব মলাটে শুধু ঢাকা পড়ে। জীর্ণ কাগজে, শীর্ণ অক্ষরে, ক্ষীণ কালিতে ছাপানো একখানি পদকপতর, যে শত শত তর্কতকে ঝকঝকে চকচকে গ্রন্থের চাইতে শতগুণ আদরের সামগ্রী।
এখন সমালোচনা শুরু করে দেবার পূর্বেই কথাটার একটু আলোচনা করা দরকার। কারণ, ঐ শব্দটি আমরা ঠিক অর্থে ব্যবহার করি কি না, সেবিষয়ে আমার একটু সন্দেহ আছে। প্রথমেই, ‘সম’-উপসর্গটির যে বিশেষ কোনো সার্থকতা আছে, এরূপ আমার বিশ্বাস নয়। শব্দ অতিকায় হলে যে তার গৌরব-বৃদ্ধি হয়, একথা আমি মানি; কিন্তু, দেহভারের সঙ্গেসঙ্গে যে বাক্যের অর্থ ভার বেড়ে যায়, তার কোনো বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ যুগের লেখকেরা মাতৃভাষায় লিখেই সন্তুষ্ট থাকেন না, কিন্তু সেইসঙ্গে মায়ের দেহপষ্টি করাও তাঁদের কর্তব্য বলে মনে করেন। কিন্তু সে পটিসাধনের জন্য বহুসংখ্যক অর্থপর্ণে ছোট-ছোট কথা চাই, যা সহজেই বঙ্গভাষার অঙ্গীভূত হতে পারে। স্বল্পসংখ্যক এবং কতকাংশে নিরর্থক বড়-বড় কথার সাহায্যে সে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হবে না। সংস্কৃতভাষার সঙ্গে আমার পরিচয় অতি সামান্য; কিন্তু সেই স্বল্প পরিচয়েই আমার এইটকু জ্ঞান জন্মেছে যে, সে ভাষার বাক্যাবলী আয়ত্ত করা নিতান্ত কঠিন। সংস্কৃতের উপর হস্তক্ষেপ করবামাত্রই তা আমাদের হস্তগত হয় না। বরং আমাদের অশিক্ষিত হাতে পড়ে প্রায়ই তার অর্থ বিকৃতি ঘটে। সংস্কৃতসাহিত্যে গোঁজামিলন-দেওয়া-জিনিসটা একেবারেই প্রচলিত ছিল না। কবি হোন, দার্শনিক হোন, আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রত্যেক কথাটি ওজন করে ব্যবহার করতেন। শব্দের কোনোরূপ অসংগত প্রয়োগ সেকালে অমার্জনীয় দোষ বলে গণ্য হত। কিন্তু একালে আমরা কথার সংখ্যা নিয়েই ব্যস্ত, তার ওজনের ধার বড়-একটা ধারি নে। নিজের ভাষাই যখন আমরা সক্ষম অর্থ বিচার করে ব্যবহার করি নে, তখন স্বল্পপরিচিত এবং অনায়ত্ত সংস্কৃত শব্দের অর্থ বিচার করে ব্যবহার করতে গেলে সে ব্যবহার যে বন্ধ হবার উপক্রম হয়, তা আমি জানি। তবুও একেবারে বেপরোয়াভাবে সংস্কৃত শব্দের অতিরিক্ত-ব্যবহারের আমি পক্ষপাতী নই। তাতে মনোভাবও স্পষ্ট করে ব্যক্ত করা যায় না, এবং ভাষাও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপে দেখানো যেতে পারে, এই সমালোচনা’-কথাটা আমরা যে অর্থে ব্যবহার করি, তার আসল অর্থ ঠিক তা নয়। আমরা কথায় বলি লেখাপড়া শিখি; কিন্তু আসলে আমরা অধিকাংশ শিক্ষিত লোক শুধু পড়তেই শিখি লিখতে শিখি নে। পাঠকমাত্রেরই পাঠ্য কিংবা অপাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে মতামত গড়ে তোলবার ক্ষমতা থাক আর না থাক, মতামত ব্যক্ত করবার অধিকার আছে; বিশেষত সে কার্যের উদ্দেশ্য যখন আর-পাঁচজনকে বই পড়ানো, লেখানো নয়। সতরাং সমালোচিতব্য বিষয়ের বাংলাসাহিত্যে অভাব থাকলেও সমালোচনার কোনো অভাব নেই। এই সমালোচনা-বন্যার ভিতর থেকে একখানিমাত্র বই উপরে ভেসে উঠেছে। সে হচ্ছে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘আলোচনা। তিনি যদি উক্ত নামের পরিবর্তে তার সমালোচনা নাম দিতেন, তাহলে, আমার বিশ্বাস, বৃথা বাগাড়ম্বরে ‘আলোচনা’র ক্ষদ্র দেহ আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে এত গরভার হয়ে উঠত যে, উক্ত শ্রেণীর আর-পাঁচখানা বইয়ের মত এখানিও বিস্মৃতির অতল জলে ডুবে যেত। এই দুটি শব্দের মধ্যে যদি একটি রাখতেই হয়, তাহলে ‘সম বাদ দিয়ে আলোচনা’ রক্ষা করাই শ্রেয়। যদিচ ওকথাটিকে আমি ইংরেজি criticism শব্দের ঠিক প্রতিবাক্য বলে মনে করি নে। আলোচনা মানে ‘আ’ অর্থাৎ বিশেষরূপে ‘লোচন’ অর্থাৎ ঈক্ষণ। যেবিষয়ে সন্দেহ হয়, তার সন্দেহভঞ্জন করবার জন্য বিশেষরূপে সেটিকে লক্ষ্য করে দেখবার নামই আলোচনা। তর্কবিতক বাগবিতণ্ডা আন্দোলন-আলোড়ন প্রভৃতি অর্থেও ঐ কথাটি আজকালকার বাংলাভাষায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু ওকথায় তার কোনো অর্থই বোঝায় না। আলোচনা’ ইংরেজি scrutinize শব্দের যথার্থ প্রতিবাক্য।Criticismশব্দের ঠিক প্রতিবাক্য বাংলা কিংবা সংস্কৃত ভাষায় না থাকলেও, ‘বিচার’ শব্দটি অনেকপরিমাণে সেই অর্থ প্রকাশ করে। কিন্তু ‘সমালোচনার পরিবতে ‘বিচার’ যে বাঙালি সমালোচকদের কাছে গ্রাহ্য হবে, এ আশা আমি রাখি নে। কারণ, এদের উদ্দেশ্য বিচার করা নয়, প্রচার করা। তাছাড়া যেকথাটা একবার সাহিত্যে চলে গেছে, তাকে অচল করবার প্রস্তাব অনেকে হয়ত দুঃসাহসিকতার পরিচয় বলে মনে করবেন। তার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, পূর্বে যখন আমরা নির্বিচারে বহুসংখ্যক সংস্কৃত শব্দকে বঙ্গসাহিত্যের কারাগারে প্রবেশ করিয়েছি, এখন আবার সুবিচার করে তার গুটিকতককে মুক্তি দেওয়াটা বোধ হয় অন্যায় কার্য হবে না। আর-এক কথা। যদি criticism অর্থেই আমরা আলোচনা শব্দ ব্যবহার করি, তাহলে scrutinize অর্থে আমরা কি শব্দ ব্যবহার করব? সুতরাং, যে উপায়ে আমরা মাতৃভাষার দেহপটি করতে চাই, তাতে ফলে শুধু তার অঙ্গহানি হয়। শব্দ সম্বন্ধে যদি আমরা একটু শুচিবাতিকগ্রস্ত হতে পারি, তাহলে, আমার বিশ্বাস, বঙ্গভাষার নির্মলতা অনেকপরিমাণে রক্ষিত হতে পারে। অনাবশ্যকে যদি আমরা সংস্কৃতভাষার উপর হস্তক্ষেপ করতে সংকুচিত হই, তাতে সংস্কৃতভাষার উপর অবজ্ঞা দেখানো হবে না, বরং তার প্রতি যথার্থ ভক্তিই দেখানো হবে। শব্দগৌরবে সংস্কৃতভাষা অতুলনীয়। কিন্তু তাই বলে তার ধনিতে মধ হয়ে আমরা যে শুধু তার সাহায্যে বাংলাসাহিত্যে ফাঁকা আওয়াজ করব, তাও ঠিক নয়। বাণী কেবলমাত্র ধ্বনি নয়। আমি বহুদিন থেকে এই মত প্রচার করে আসছি, কিন্তু আমার কথায় কেউ কর্ণপাত করেন না। সাহিত্যজগতে একশ্রেণীর জীব বিচরণ করে, যাদের প্রাণের চাইতে কান বড়। সংগীতচর্চার লোভ তারা কিছুতেই সংবরণ করতে পারে না, এবং সে ব্যাপার থেকে তাদের নিরস্ত করবার ক্ষমতাও কারও নেই। প্রতিবাদ করায় বিশেষ-কোনো ফল নেই জেনেও আমি প্রতিবাদ করি; কারণ, আজকালকার মতে, আপত্তি নিশ্চিত অগ্রাহ্য হবে জেনেও আপত্তি করে আপত্তিকর জিনিসটে সম্পূর্ণ গ্রাহ্য করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য বলে বিবেচিত হয়।
এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে, কোনো বিশেষ লেখকের বা লেখার প্রতি কটাক্ষ করে আমি এসব কথা বলছি নে। বাংলাসাহিত্যের একটা প্রচলিত ধরন ফ্যাশান এবং ঢঙের সম্বন্ধেই আমার আপত্তি, এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করাই আমার উদ্দেশ্য। সমাজের কোনো চলতি স্রোতে গা ঢেলে দিয়ে যে আমরা কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পারি, এমন অন্যায় ভরসা আমি রাখি নে। সকল উন্নতির মূলে থামা-জিনিসটে বিদ্যমান। এ পৃথিবীতে এমনকোনো সিড়ি নেই, যার ধাপে ধাপে পা ফেলে আমরা অবলীলাক্রমে স্বর্গে গিয়ে উপস্থিত হতে পারি। মনোজগতে প্রচলিত পথ ক্রমে সংকীর্ণ হতে সংকীর্ণতর হয়ে শেষে চোরাগলিতে পরিণত হয়, এবং মানুষের গতি আটকে দেয়। বিজ্ঞানে যাকে ইভলিউশন বলে, এককথায় তার পদ্ধতি এই যে, জীব একটা প্রচলিত পথে চলতে চলতে হঠাৎ এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে ডাইনে কি বাঁয়ে একটা নতুন পথ আবিষ্কার করে এবং সাহস করে সেই পথে চলতে আরম্ভ করে। এই নতুন পথ বার করা, এবং সেই পথ ধরে চলার উপরেই জীবের জীবন এবং মানুষের মনুষ্যত্ব নির্ভর করে। মুক্তির জন্যে, হয় দক্ষিণ নয় বাম মাগ যে অবলম্বন করতেই হবে, একথা এদেশে ঋষিমুনিরা বহুকাল পূর্বে বলে গেছেন; অতএব একেলে বিজ্ঞান এবং সেকেলে দর্শন উভয়ই এই শিক্ষা দেয় যে, সিধে পথটাই মৃত্যুর পথ। সুতরাং বাংলা লেখার প্রচলিত পথটা ছাড়তে পরামর্শ দিয়ে আমি কাউকে বিপথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করি নে। আমার বিশ্বাস যে, সংস্কৃত ছেড়ে যদি আমরা দেশী পথে চলতে শিখি, তাতে বাংলাসাহিত্যের লাভ বই লোকসান নেই। ঐ পথটাই তো স্বাধীনতার পথ, এবং সেই কারণেই উন্নতির পথ— এই ধারণাটি মনে এসে যাওয়াতেও আমাদের অনেক উপকার আছে। আমি জানি যে, সাহিত্যে কিংবা ধর্মে একটা নতুন পথ আবিষ্কার করবার ক্ষমতা কেবলমাত্র দু-চারজন মহাজনেরই থাকে, বাদবাকি আমরা পাঁচজনে সেই মহাজন-প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করে চলতে পারলেই আমাদের জীবন সার্থক হয়। গড্ডলিকাপ্রবাহ ন্যায়ের অবলম্বন করা জনসাধারণের পক্ষে স্বাভাবিকও বটে, কর্তব্যও বটে; কেননা, পৃথিবীর সকল ভেড়াই যদি মেড়া হয়ে ওঠে তো ঢুঁ-মারামারি করেই মেষ-বংশ নির্বংশ হবে। উক্ত কারণেই আমি লেখবার একটা প্রচলিত ধরনের বিরোধী হলেও প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের বিরোধী নই। আমরা কেউ ভাষা-জিনিসটে তৈরি করি নে, সকলেই তৈরি ভাষা ব্যবহার করি। ভাষা-জিনিসটে কোনো-একটি বিশেষ ব্যক্তির মনগড়া নয়, যুগযুগান্তর ধরে একটি জাতির হাতে-গড়া। কেবলমাত্র মনোমত কথা বেছে নেবার, এবং ব্যাকরণের নিয়মরক্ষা করে সেই বাছাই কথাগলিকে নিজের পছন্দমত পাশাপাশি সাজিয়ে রাখবার স্বাধীনতাই আমাদের আছে। আমাদের মধ্যে যাঁরা জহরি, তাঁরা এই চলতি কথার মধ্যেই রত্ন আবিষ্কার করেন, এবং শিল্পগুণে গ্রথিত করে দিব্য হার রচনা করেন। নিজের রচনাশক্তির দারিদ্র্যের চেহারাই আমরা মাতৃভাষার মুখে দেখতে পাই, এবং রাগ করে সেই আয়নাখানিকে নষ্ট করতে উদ্যত হই ও পূর্বপুরুষদের সংস্কৃত পণের সাহায্যে মুখরক্ষা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠি। একরকম কাঁচ আছে, যাতে মুখ মস্ত দেখায়, কিন্তু সেইসঙ্গে চেহারা অপরিচিত বিকটাকার ধারণ করে। আমাদের নিজেকে বড় দেখাতে গিয়ে যে আমরা কিম্ভূতকিমাকার রূপ ধারণ করি, তাতে আমাদের কোনো লজ্জাবোধ হয় না। এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, প্রচলিত ভাষা কাকে বলে। তার উত্তরে আমি বলি, যে ভাষা আমাদের সুপরিচিত, সম্পূর্ণ আয়ত্ত, এবং যা আমরা নিত্য ব্যবহার করে থাকি। তা খাঁটি বাংলাও নয়, খাঁটি সংস্কৃতও নয়, কিংবা উভয়ে মিলিত কোনোরূপ খিচুড়িও নয়। যে সংস্কৃত শব্দ প্রকৃত কিংবা বিকৃত রূপে বাংলা কথার সঙ্গে মিলেমিশে রয়েছে, সে শব্দকে আমি বাংলা বলেই জানি এবং মানি। কিন্তু কেবলমাত্র নতুনত্বের লোভে নতুন করে যেসকল সংস্কৃত শব্দকে কোনো লেখক জোর করে বাংলাভাষার ভিতর প্রবেশ করিয়েছেন, অথচ খাপ খাওয়াতে পারেন নি, সেইসকল শব্দকে ছতে আমি ভয় পাই। এবং যেসকল সংস্কৃত শব্দ স্পষ্টত ভুল অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেইসকল শব্দ যাতে ঠিক অর্থে ব্যবহত হয়, সেবিষয়ে আমি লেখকদের সতর্ক হতে বলি। নইলে বঙ্গভাষার বনলতা যে সংস্কৃতভাষার উদ্যানলতাকে তিরস্কৃত করবে, এমন দুরাশা আমার মনে স্থান পায় না। শব্দকল্পদ্রুম থেকে আপনা হতে খসে যা আমাদের কোলে এসে পড়েছে, তা মুখে তুলে নেবার পক্ষে আমার কোনো আপত্তি নেই। তলার কুড়োও, কিন্তু সেইসঙ্গে গাছেরও পেড়ো না। তাতে যে পরিমাণ পরিশ্রম হবে, তার অনুরূপ ফললাভ হবে না।
শুধু গাছ থেকে পাড়া নয়, একেবারে তার আগডাল থেকে পাড়া গুটিকতক শব্দের পরিচয় আমি সম্প্রতি বইয়ের মলাটে পেয়েছি। এবং সে সম্বন্ধে আমার দু-একটি কথা বক্তব্য আছে। যাঁরা ‘শব্দাধিক্যাৎ অর্থাধিক্যং’ মীমাংসার এই নিয়ম মানেন না, বরং তার পরিবর্তে সংস্কৃত শব্দ সম্বন্ধে ‘অধিকন্তু ন দোষায়’— এই উদ্ভট বচন অনুসারে কার্যানুবর্তী হয়ে থাকেন, তাঁরাও একটা গণ্ডির ভিতর থেকে বেরিয়ে যেতে সাহসী হন না। এমন সাহিত্য-বীর বোধ হয় বাংলাদেশে খুব কম আছে, যারা বঙ্গরমণীর মাথায় ধম্মিল্ল চাপিয়ে দিতে সংকুচিত না হয়, যদি সে বেচারারা নীরবে পুরুষের সব অত্যাচারই সহ্য করে থাকে। বঙ্কিমী যুগে সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার কিছু, কম ছিল না। অথচ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রও ‘প্রাড়বিবাক’ বাক্যটি ‘মলিম্লুচে’র ন্যায় কটু ভাষার হিসাবে গণ্য করে চোর এবং বিচারপতিকে একই আসনে বসিয়ে দিয়েছিলেন। ‘প্রাড়বিবাক’ বেচারা বাঙালিজাতির নিকট এতই অপবিচিত ছিল যে, বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে তার ঐরূপ লাঞ্ছনাতেও কেউ আপত্তি করে নি। কিন্তু আজকাল ওর চাইতেও অপরিচিত শব্দও নতুন গ্রন্থের বক্ষে কৌস্তুভমণির মত বিরাজ করতে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি দু-একটির উল্লেখ করব।
শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল জাতকবি। তাঁর ভালো-মন্দ-মাঝারি সকল কবিতাতেই তাঁর কবির জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। বোধ হয় তাঁর রচিত এমন-একটি কবিতাও নেই, যার অন্তত একটি চরণেও ধ্বজবজ্রাঙ্কুশের চিহ্ন না লক্ষিত নয়। সত্যের অনুরোধে একথা আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে, তাঁর নতুন পুস্তকের নামটিতে আমার একটু খটকা লেগেছিল। ‘এষা’ শব্দের সঙ্গে আমার ইতিপূর্বে কখনো দেখা-সাক্ষাৎ হয় নি, এবং তার নামও আমি পূর্বে কখনো শুনি নি। কাজেই আমার প্রথমেই মনে হয়েছিল যে, হয়ত ‘আয়েষা’ নয়ত ‘এশিয়া’ কোনোরূপ ছাপার ভুলে ‘এষা’-রপ ধারণ করেছে। আমার এরূপ সন্দেহ হবার কারণও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র যখন আয়েষাকে নিয়ে নভেল লিখেছেন, তখন তাকে নিয়ে অক্ষয়কুমার যে কবিতা রচনা করবেন, এতে আর আশ্চর্য হবার কারণ কি থাকতে পারে। আবার বলি ওসমান! এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর।’— এই পদটির উপর রমণীহদয়ের সপ্তকাণ্ড-রামায়ণ খাড়া করা কিছু কঠিন নয়। তারপর ‘এশিয়া’, প্রাচীর এই নবজাগরণের দিনে তার প্রাচীন নিদ্রাভঙ্গ করবার জন্য যে কবি উৎসুক হয়ে উঠবেন, এও তো স্বাভাবিক। যার ঘুম সহজে ভাঙে না, তার ঘুম ভাঙাবার দুটিমাত্র উপায় আছে–হয় টেনে-হিঁচড়ে, নয় ডেকে। এশিয়ার ভাগ্যে টানাহেঁচড়ানো-ব্যাপারটা তো পুরোদমে চলছে, কিন্তু তাতেও যখন তার চৈতন্য হল না, তখন ডাকা ছাড়া আর কি উপায় আছে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা এশিয়াকে কাব্যে দর্শনে নানারূপ ঘুমপাড়ানি-মাসিপিসির গান গেয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেছেন। এখন আবার জাগাতে হলে এ যুগের কবিরা ‘জাগর’-গান গেয়েই তাকে জাগাতে পারবেন। সে গান অনেক কবি সুরে-বেসুরে গাইতেও শুরু করে দিয়েছেন। সুতরাং আমার সহজেই মনে হয়েছিল যে, অক্ষয়কুমার বড়ালও সেই কার্যে ব্রতী হয়েছেন। কিন্তু এখন শুনছি যে, ও ছাপার ভুল নয়, আমারই ভুল। প্রাচীন গাঁথার ভাষায় নাকি ‘এষা’র অর্থ অন্বেষণ। একালের লেখকেরা যদি শব্দের অন্বেষণে সংস্কৃতযুগ ডিঙিয়ে একেবারে প্রাচীন গাঁথা-যুগে গিয়ে উপস্থিত হন, তাহলে একেলে বঙ্গ-পাঠকদের উপর একটু অত্যাচার করা হয়; কারণ, সেই শব্দের অর্থ-অন্বেষণে পাঠক যে কোন দিকে যাবে, তা স্থির করতে পারে না। আজকালকার বাংলা বুঝতে অমরের সাহায্য আবশ্যক, তারপর যদি আবার যাস্ক চর্চা করতে হয়, তাহলে বাংলাসাহিত্য পড়বার অবসর আমরা কখন পাব? যাস্কের সাহায্যেও যদি তার অর্থবোধ না হয়, তাহলে বাংলাসাহিত্যের চর্চা যে আমরা ত্যাগ করব, তাতে আর সন্দেহ কি। অর্থবোধ হয় না বলে যখন আমরা আমাদের পরকালের সম্পতির একমাত্র সহায় যে সন্ধ্যা, তারই পাঠ বন্ধ করেছি, তখন ইহকালের ক্ষণিক সুখের লোভে যে আমরা গাঁথার শব্দে রচিত বাংলাসাহিত্য পড়ব, এ আশা করা যেতে পারে না। তাছাড়া বৈদিক এবং অতিবৈদিক ভাষা থেকে যদি আমরা বাক্যসংগ্রহ করতে আরম্ভ করি, তাহলে তান্ত্রিক ভাষাকেই বা ছাড়ব কেন। আমার লিখিত নতুন বইখানির নাম যদি আমি ‘ফেৎকারিণী’ ‘ডামর’ কিংবা ‘উড্ডীশ’ দিই, তাহলে কি পাঠকসম্প্রদায় খুব খুশি হবেন?
শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পুস্তিকাগুলির নামকরণবিষয়ে যে অপূর্বতা দেখিয়ে থাকেন, তা আমাকে ভীত না করুক, বিস্মিত করে। আমি সাহিত্যের বাজারে মাল যাচাই করবার জন্য কষ্টিপাথর হাতে নিয়ে ব্যাবসা খুলে বসি নি। সুতরাং সুধীন্দ্রবাবুর রচনার দোষগুণ দেখানো আমার কর্তব্যের মধ্যে নয়। একমাত্র মলাটে তাঁর লেখা যেটকু আত্মপরিচয় দেয়, সেইটকু আমার বিচারাধীন। ‘মঞ্জষা করঙ্ক’ প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে যে আমাদের একেবারে মুখ দেখাদেখি নেই, একথা বলতে পারি নে। তাহলেও স্বীকার করতে হবে যে, অন্তত পাঠিকাদের নিকট ও পদার্থগলি যত সুপরিচিত, ও নামগুলি তাদশ নয়। তাছাড়া ঐরূপ নামের যে বিশেষ কোনো সার্থকতা আছে, তাও আমার মনে হয় না। আমাদের কল্পনাজাত বস্তু আমরা প্যাটরায় পরে সাধারণের কাছে দিই নে, বরং সত্যকথা বলতে গেলে মনের প্যাটরা থেকে সেগুলি বার করে জনসাধারণের চোখের সম্মুখে সাজিয়ে রাখি। করল্কের কথা শুনলেই তালের কথা মনে হয়। পানের খিলির সঙ্গে সুধীন্দ্রবাবুর ছোটগল্পগুলির কি সাদশ্য আছে, জানি নে। করণ রস এবং পানের রস এক জিনিস নয়। আর-একটি কথা। তাম্বুলের সঙ্গেসঙ্গে চর্বিতচর্বণের ভাবটা মানুষের মনে সহজেই আসে। সে যাই হোক, আমি লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করছি যে, সুধীন্দ্রবাবুর আবিষ্কৃত ‘বৈতানিক’ শব্দ আমি বৈতালিক শব্দের ছাপান্তর মনে করেছিলাম। হাজারে ন-শ-নিরানব্বই জন বাঙালি পাঠক যে ও শব্দের অর্থ জানেন না, একথা বোধ হয় সুধীন্দ্রবাবু অস্বীকার করবেন না। আমার যতদূর মনে পড়ে তাতে কেবলমাত্র ভৃগুপোক্ত মানব-ধর্মশাস্ত্রে এক স্থলে ঐ শব্দটির ব্যবহার দেখেছি। কিন্তু তার অর্থ জানা আবশ্যক মনে করি নি। এইরূপ নামে বইয়ের পরিচয় দেওয়া হয় না, বরং তার পরিচয় গোপন করাই হয়। বাংলা-সরস্বতীকে ছদ্মবেশ না পরালে যে তাঁকে সমাজে বার করা চলে না, একথা আমি মানি নে।
এই নামের উদাহরণক’টি টেনে আনবার উদ্দেশ্য, আমার সেই প্রথম কথার প্রমাণ দেওয়া। সেকথা এই যে, বঙ্গসাহিত্যের ভিতর সমালোচনার মত নামকরণেও বিজ্ঞাপনের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। বিজ্ঞাপনের আরপাঁচটা দোষের ভিতর একটা হচ্ছে তার ন্যাকামি। ন্যাকামির উদ্দেশ্য হচ্ছে সহজে লোকপ্রিয় হওয়া, এবং তার লক্ষণ হচ্ছে ভাবে এবং ভাষায় মাধুর্যের ভান এবং ভঙ্গি। বঙ্গসাহিত্যে ক্ৰমে যে তাই প্রশ্রয় পাচ্ছে, সেইটে দেখিয়ে দেবার জন্যে আমার এত কথা বলা। আমরা এতটাই কোমলের ভক্ত হয়ে পড়েছি যে, শুদ্ধ স্বরকেও কোমল করতে গিয়ে বিকৃত করতে আমরা তিলমাত্র দ্বিধা করি নে। কথায় বলে, ‘যত চিনি দেবে ততই মিষ্টি হবে’। কিন্তু শর্করার ভাগ অতিরিক্ত হলে মিষ্টান্নও যখন অখাদ্য হয়ে ওঠে, তাতে আর সন্দেহ কি। লেখকেরা যদি ভাষাকে সুকুমার করবার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে তাকে সুস্থ এবং সবল করবার চেষ্টা করেন, তাহলে বঙ্গসাহিত্যে আবার প্রাণ দেখা দেবে। ভাষা যদি প্রসন্ন হয়, তাহলে তার কর্কশতাও সহ্য হয়। এ এতই সোজা কথা যে, এও যে আবার লোককে বোঝাতে হয়, এই মহা আপসোসের বিষয়। যখন বঙ্গসাহিত্যে অন্ধকার আর ‘বিরাজ’ করবে না, তখন এবিষয়ে আর কারও ‘মনোযোগ আকর্ষণ’ করবার দরকারও হবে না।
অগ্রহায়ণ ১৩১৯
যৌবনে দাও রাজটিকা
গতমাসের সবুজপত্রে শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যৌবনকে রাজটিকা দেবার প্রস্তাব করেছেন। আমার কোনো টীকাকার বন্ধ এই প্রস্তাবের বক্ষ্যমাণরূপ ব্যাখ্যা করেছেন–
যৌবনকে টিকা দেওয়া অবশ্যকর্তব্য, তাহাকে বসন্তের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য। এস্থলে রাজটিকা অর্থ রাজা অর্থাৎ যৌবনের শাসনকর্তাকর্তৃক তাহার উপকারার্থে দত্ত যে টিকা, সেই টিকা। উক্তপদ তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাসে সিদ্ধ হইয়াছে।
উল্লিখিত ভাষ্য আমি রহস্য বলে মনে করতুম, যদি-না আমার জানা থাকত যে, এদেশে জ্ঞানীব্যক্তিদিগের মতে মনের বসন্তঋতু ও প্রকৃতির যৌবনকাল –দুই অশায়েস্তা, অতএব শাসনযোগ্য। এ উভয়কে জড়িতে জতলে আর বাগ মানানো যায় না; অতএব এদের প্রথমে পথক করে পরে পরাজিত করতে হয়।
বসন্তের স্পর্শে ধরণীর সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে; অবশ্য তাই বলে পৃথিবী তার আলিঙ্গন হতে মুক্তিলাভ করবার চেষ্টা করে না, এবং পোষমাসকেও বারোমাস পষে রাখে না। শীতকে অতিক্রম করে বসন্তের কাছে আত্মসমর্পণ করায় প্রকৃতি যে অর্বাচীনতার পরিচয় দেয় না, তার পরিচয় ফলে।
প্রকৃতির যৌবন শাসনযোগ্য হলেও তাকে শাসন করবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই; কেননা, প্রকৃতির ধর্ম মানবধর্মশাস্ত্রবহির্ভূত। সেই কারণে জ্ঞানীব্যক্তিরা আমাদের প্রকৃতির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করতে বারণ করেন, এবং নিত্যই আমাদের প্রকৃতির উলটো টান টানতে পরামর্শ দেন; এই কারণেই মানুষের যৌবনকে বসন্তের প্রভাব হতে দরে রাখা আবশ্যক। অন্যথা, যৌবন ও বসন্ত এ দুয়ের আবির্ভাব যে একই দৈবীশক্তির লীলা–এইরূপ একটি বিশ্বাস আমাদের মনে স্থানলাভ করতে পারে।
এদেশে লোকে যে যৌবনের কপালে রাজটিকার পরিবর্তে তার পঠে রাজদণ্ড প্রয়োগ করতে সদাই প্রস্তুত, সেবিষয়ে আর-কোনো সন্দেহ নেই। এর কারণ হচ্ছে যে, আমাদের বিশ্বাস মানবজীবনে যৌবন একটা মস্ত ফাঁড়া কোনোরকমে সেটি কাটিয়ে উঠতে পারলেই বাঁচা যায়। এ অবস্থায় কি জ্ঞানী, কি অজ্ঞানী সকলেই চান যে, একলম্ফে বাল্য হতে বার্ধক্যে উত্তীর্ণ হন। যৌবনের নামে আমরা ভয় পাই, কেননা তার অন্তরে শক্তি আছে। অপরপক্ষে বালকের মনে শক্তি নেই, বালকের জ্ঞান নেই, বন্ধের প্রাণ নেই। তাই আমাদের নিয়ত চেষ্টা হচ্ছে, দেহের জড়তার সঙ্গে মনের জড়তার মিলন করা, অজ্ঞতার সঙ্গে বিজ্ঞতার সন্ধিস্থাপন করা। তাই আমাদের শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে ইচড়ে পাকানো, আর আমাদের সমাজনীতির উদ্দেশ্য হচ্ছে জাগ দিয়ে পাকানো।
আমাদের উপরোক্ত চেষ্টা যে ব্যর্থ হয় নি, তার প্রমাণ আমাদের সামাজিক জীবন। আজকের দিনে এদেশে রাজনীতির ক্ষেত্রে একদিকে বালক, অপরদিকে বদ্ধ; সাহিত্যক্ষেত্রে একদিকে স্কুলবয়, অপর দিকে স্কুলমাস্টার; সমাজে একদিকে বাল্যবিবাহ, অপরদিকে অকালমৃত্যু; ধর্মক্ষেত্রে একদিকে শুধু ইতি ইতি’, অপরদিকে শুধু নেতি নেতি’; অর্থাৎ একদিকে লোষ্ট্রকাঠও দেবতা, অপরদিকে ঈশ্বরও ব্রহ্ম নন। অর্থাৎ আমাদের জীবনগ্রন্থে প্রথমে ভূমিকা আছে, শেষে উপসংহার আছে; ভিতরে কিছু নেই। এ বিশ্বের জীবনের আদি নেই, অন্ত নেই, শুধু মধ্য আছে; কিন্তু তারই অংশীভূত আমাদের জীবনের আদি আছে, অন্ত আছে; শুধু মধ্য নেই।
বার্ধক্যকে বাল্যের পাশে এনে ফেললেও আমরা তার মিলন সাধন করতে পারি নি; কারণ ক্রিয়া বাদ দিয়ে দুটি পদকে জুড়ে এক করা যায় না। তাছাড়া যা আছে, তা নেই বললেও তার অস্তিত্ব লোপ হয়ে যায় না। এ বিশ্বকে মায়া বললেও তা অস্পৃশ্য হয়ে যায় না, এবং আত্মাকে ছায়া বললেও তা অদশ্য হয়ে যায় না। বরং কোনো-কোনো সত্যের দিকে পিঠ ফেরালে তা অনেক সময়ে আমাদের ঘাড়ে চড়ে বসে। যে যৌবনকে আমরা সমাজে স্থান দিই নি, তা এখন নানা বিকৃতরূপে নানা ব্যক্তির দেহ অবলম্বন করে রয়েছে। যাঁরা সমাজের সম্মুখে জীবনের শুধু নান্দী ও ভরতবচন পাঠ করেন, তাঁদের জীবনের অভিনয়টা যবনিকার অন্তরালেই হয়ে থাকে। রদ্ধ ও বন্ধ করে রাখলে পদার্থ মাত্রই আলোর ও বায়ুর সম্পর্ক হারায়, এবং সেইজন্য তার গায়ে কলঙ্ক ধরাও অনিবার্য। গুপ্ত জিনিসের পক্ষে দুষ্ট হওয়া স্বাভাবিক।
আমরা যে যৌবনকে গোপন করে রাখতে চাই, তার জন্য আমাদের প্রাচীন সাহিত্য অনেক পরিমাণে দায়ী। কোনো বিখ্যাত ইংরেজ লেখক বলেন যে, literature হচ্ছে criticism of life; ইংরেজিসাহিত্য জীবনের সমালোচনা হতে পারে, কিন্তু সংস্কৃতসাহিত্য হচ্ছে যৌবনের আলোচনা।
সংস্কৃতসাহিত্যে যুবকযুবতী ব্যতীত আর কারও স্থান নেই। আমাদের কাব্যরাজ্য হচ্ছে সূর্যবংশের শেষ নপতি অগ্নিবর্ণের রাজ্য, এবং সেদেশ হচ্ছে অষ্টাদশবর্ষদেশীয়াদের স্বদেশ। যৌবনের যে ছবি সংস্কৃত দশ্যেকাব্যে ফটে উঠেছে, সে হচ্ছে ভাৈগবিলাসের চিত্র। সংস্কৃতকাব্যজগৎ মাল্যচন্দনবনিতা দিয়ে গঠিত এবং সে জগতের বনিতাই হচ্ছে স্বর্গ, ও মাল্যচন্দন তার উপসর্গ।
এ কাব্যজগতের স্রষ্টা কিংবা দ্রষ্টা কবিদের মতে প্রকৃতির কাজ হচ্ছে শুধু রমণীদেহের উপমা যোগানো, এবং পুরুষের কাজ শুধু রমণীর মন যোগানো। হিন্দুযুগের শেষকবি জয়দেব নিজের কাব্যসম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে যেকথা বলেছেন, তাঁর পববতী কবিরাও ইঙ্গিতে সেই একই কথা বলেছেন। সেকথা এই যে, যদি বিলাস-কলায় কুতুহলী হও তো আমার কোমলকান্ত পদাবলী শ্রবণ করো’। এককথায় যে-যৌবন য্যাতি নিজের পুত্রদের কাছে ভিক্ষা করেছিলেন, সংস্কৃতকবিরা সেই যৌবনেরই রূপগুণ বর্ণনা করেছেন।
একথা যে কত সত্য, তা একটি উদাহরণের সাহায্যে প্রমাণ করা যেতে পারে। কৌশাবির যুবরাজ উদয়ন এবং কপিলবার যুবরাজ সিদ্ধার্থ উভয়ে সমসাময়িক ছিলেন। উভয়েই পরম রূপবান এবং দিব্য শক্তিশালী যুবাপুরুষ; কিন্তু উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এইটুকু যে, একজন হচ্ছেন ভোগের আর একজন হচ্ছেন ত্যাগের পর্ণ অবতার। ভগবান গৌতমবুদ্ধের জীবনের ব্রত ছিল মানবের মোহনাশ করে তাকে সংসারের সকল শখল হতে মুক্ত করা; আর বৎসরাজ উদয়নের জীবনের ব্রত ছিল ঘোষবতী বীণার সাহায্যে অরণ্যের গজকামিনী এবং অন্তঃপুরের গজগামিনীদের প্রথমে মদ্ধে ক’রে পরে নিজের ভোগের জন্য তাদের অবরুদ্ধ করা। অথচ সংস্কৃতকাব্যে বন্ধচরিতের স্থান নেই, কিন্তু উদয়নকথায় তা পরিপূর্ণ।
সংস্কৃতভাষায় যে বুদ্ধের জীবনচরিত লেখা হয় নি, তা নয়; তবে ললিতবিস্তরকে আর-কেউ কাব্য বলে স্বীকার করবেন না, এবং অশ্বঘোষের নাম পর্যন্তও লুপ্ত হয়ে গেছে। অপরদিকে উদয়ন-বাসবদত্তার কথা অবলম্বন করে যাঁরা কাব্যরচনা করেছেন, যথা ভাস গুণাঢ্য সবন্ধ, ও শ্রীহর্ষ ইত্যাদি, তাঁদের বাদ দিলে সংস্কৃতসাহিত্যের অর্ধেক বাদ পড়ে যায়। কালিদাস বলেছেন যে, কৌশারি গ্রামবন্ধেরা উদয়নকথা শুনতে ও বলতে ভালোবাসতেন; কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কেবল কৌশারি গ্রামবদ্ধ কেন, সমগ্র ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ঐ কথা-রসের রসিক। সংস্কৃতসাহিত্য এ সত্যের পরিচয় দেয় না যে, বন্ধের উপদেশের বলে জাতীয় জীবনে যৌবন এনে দিয়েছিল, এবং উদয়নের দ্রষ্টান্তের ফলে অনেকের যৌবনে অকালবার্ধক্য এনে দিয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের অনুশীলনের ফলে রাজা অশোক লাভ করেছিলেন সাম্রাজ্য; আর উদয়নধর্মের অনুশীলন করে রাজা অগ্নিবর্ণ লাভ করেছিলেন রাজক্ষমা। সংস্কৃতকবিরা এ সত্যটি উপেক্ষা করেছিলেন যে, ভোগের ন্যায় ত্যাগও যৌবনেরই ধর্ম। বার্ধক্য কিছু অর্জন করতে পারে না বলে কিছু বর্জনও করতে পারে না। বার্ধক্য কিছু কাড়তে পারে না বলে কিছু ছাড়তেও পারে না— দুটি কালো চোখের জন্যও নয়, বিশকোটি কালো লোকের জন্যও নয়।
পাছে লোকে ভুল বোঝেন বলে এখানে আমি একটি কথা বলে রাখতে চাই। কেউ মনে করবেন না যে, আমি কাউকে সংস্কৃতকাব্য বয়কট করতে বলছি কিংবা নীতি এবং রচির দোহাই দিয়ে সে কাব্যের সংশোধিত সংস্করণ প্রকাশ করবার পরামর্শ দিচ্ছি। আমার মতে যা সত্য তা গোপন করা সুনীতি নয় এবং তা প্রকাশ করাও দুর্নীতি নয়। সংস্কৃতকাব্যে যে যৌবনধর্মের বর্ণনা আছে তা যে সামান্য মানবধর্ম— এ হচ্ছে অতি স্পষ্ট সত্য; এবং মানবজীবনের উপর তার প্রভাব যে অতি প্রবল— তাও অস্বীকার করবার জো নেই।
তবে এই একদেশদর্শিতা ও অত্যুক্তি— ভাষায় যাকে বলে একরোখামি ও বাড়াবাড়ি তাই হচ্ছে সংস্কৃতকাব্যের প্রধান দোষ। যৌবনের স্থূল-শরীরকে অত আশকারা দিলে তা উত্তরোত্তর স্থূল হতে স্থূলতর হয়ে ওঠে, এবং সেইসঙ্গে তার সক্ষ-শরীরটি সক্ষম হতে এত সক্ষম হয়ে উঠে যে, তা খুঁজে পাওয়াই ভার হয়। সংস্কৃতসাহিত্যের অবনতির সময়, কাব্যে রক্তমাংসের পরিমাণ এত বেড়ে গিয়েছিল যে, তার ভিতর আত্মার পরিচয় দিতে হলে সেই রক্তমাংসের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা ছাড়া আর আমাদের উপায় নেই। দেহকে অতটা প্রাধান্য দিলে মন-পদার্থটি বিগড়ে যায়; তার ফলে দেহ ও মন পথক হয়ে যায় এবং উভয়ের মধ্যে আত্মীয়তার পরিবর্তে জ্ঞাতিশত্রতা জন্মায়। সম্ভবত বৌদ্ধধর্মের নিরামিষের প্রতিবাদস্বরূপ হিন্দু, কবিরা তাঁদের কাব্যে এতটা আমিষের আমদানি করেছিলেন। কিন্তু যে কারণেই হোক প্রাচীন ভারতবর্ষের চিন্তার রাজ্যে দেহমনের পরস্পরের যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল, তার প্রমাণ প্রাচীন সমাজের একদিকে বিলাসী অপরদিকে সন্ন্যাসী, একদিকে পত্তন অপরদিকে বন, একদিকে রঙ্গালয় অপরদিকে হিমালয়; এককথায় একদিকে কামশাস্ত্র অপরদিকে মোক্ষশাস্ত্র। মাঝামাঝি আর-কিছু, জীবনে থাকতে পারত কিন্তু সাহিত্যে নেই। এবং এ দুই বিরুদ্ধ-মনোভাবের পরস্পরমিলনের যে কোনো পন্থা ছিল না, সেকথা ভর্তৃহরি স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন–
‘একা ভার্যা সুন্দরী বা দরী বা’
এই হচ্ছে প্রাচীনযুগের শেষকথা। যাঁরা দরী-প্রাণ তাঁদের পক্ষে যৌবনের নিন্দা করা যেমন স্বাভাবিক, যাঁরা সন্দরী-প্রাণ তাঁদের পক্ষেও তেমনি স্বাভাবিক। যতির মুখের যৌবন-নিন্দা অপেক্ষা কবির মুখের যৌবননিন্দার, আমার বিশ্বাস, অধিক ঝাঁঝ আছে। তার কারণ, ত্যাগীর অপেক্ষা ভোগীরা অভ্যাসবশত কথায় ও কাজে বেশি অসংযত।
যাঁরা স্ত্রীজাতিকে কেবলমাত্র ভোগের সামগ্রী মনে করেন, তাঁরাই যে শ্ৰী-নিন্দার ওস্তাদ— এর প্রমাণ জীবনে ও সাহিত্যে নিত্য পাওয়া যায়।
স্ত্রী-নিন্দুকের রাজা হচ্ছেন রাজকবি ভর্তৃহরি ও রাজকবি সোলোমন। চরম ভোগবিলাসে পরম চরিতার্থতা লাভ করতে না পেরে এরা শেষবয়সে স্ত্রীজাতির উপর গায়ের ঝাল ঝেড়েছেন। যাঁরা বনিতাকে মাল্যচন্দনহিসাবে ব্যবহার করেন, তাঁরা শুকিয়ে গেলে সেই বনিতাকে মাল্যচন্দনের মতই ভূতলে নিক্ষেপ করেন, এবং তাকে পদদলিত করতেও সংকুচিত হন না। প্রথমবয়সে মধুর রস অতিমাত্রায় চর্চা করলে শেষবয়সে জীবন তিতো হয়ে ওঠে। এ শ্রেণীর লোকের হাতে শগার-শতকের পরেই বৈরাগ্য-শতক রচিত হয়।
একই কারণে, যাঁরা যৌবনকে কেবলমাত্র ভোগের উপকরণ মনে করেন, তাঁদের মুখে যৌবন-নিন্দা লেগে থাকবারই কথা। যাঁরা যৌবন-জোয়ারে গা-ভাসিয়ে দেন, তাঁরা ভাটার সময় পাঁকে পড়ে গত জোয়ারের প্রতি কটুকাটব্য প্রয়োগ করেন। যৌবনের উপর তাঁদের রাগ এই যে, তা পালিয়ে যায় এবং একবার চলে গেলে আর ফেরে না। যযাতি যদি পরের কাছে ভিক্ষা করে যৌবন ফিরে না পেতেন, তাহলে তিনি যে কাব্য কিংবা ধর্মশাস্ত্র রচনা করতেন, তাতে যে কি সুতীব্র যৌবননিন্দা থাকত— তা আমরা কল্পনাও করতে পারি নে। পর, যে পিতৃভক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, তার ভিতর পিতার প্রতি কতটা ভক্তি ছিল এবং তাতে পিতারই যে উপকার করা হয়েছিল, তা বলতে পারি নে, কিন্তু তাতে দেশের মহা অপকার হয়েছে; কারণ নীতির একখানা বড় গ্রন্থ মারা গেছে।
যযাতি-কাঙ্ক্ষিত যৌবনের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তা অনিত্য। এবিষয়ে ব্রাহণ ও শ্রমণ, নগ্নক্ষপণক ও নাগরিক, সকলেই একমত।
যৌবন ক্ষণস্থায়ী— এই আক্ষেপে এদেশের কাব্য ও সংগীত পরিপূর্ণ–
‘ফাগুন গয়ী হয়, বহরা ফিরি আয়ী হয়
গয়ে রে যোবন, ফিরি আওত নাহি’
এই গান আজও হিন্দুস্থানের পথে-ঘাটে অতি করুণ সুরে গাওয়া হয়ে থাকে। যৌবন যে চিরদিন থাকে না, এ আপসোস রাখবার স্থান ভারতবর্যে নেই।
যা অতি প্রিয় এবং অতি ক্ষণস্থায়ী, তার স্থায়িত্ব বাড়াবার চেষ্টা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। সম্ভবত নিজের অধিকার বিস্তার করবার উদ্দেশ্যেই এদেশে যৌবন শৈশবের উপর আক্রমণ করেছিল। বাল্যবিবাহের মূলে হয়ত এই যৌবনের মেয়াদ বাড়াবার ইচ্ছাটাই বর্তমান। জীবনের গতিটি উলটো দিকে ফেরাবার ভিতরও একটা মহা আর্ট আছে। পৃথিবীর অপরসব দেশে লোকে গাছকে কি করে বড় করতে হয় তারই সন্ধান জানে, কিন্তু গাছকে কি করে ছোট করতে হয় সে কৌশল শুধু জাপানিরাই জানে। একটি বটগাছকে তারা চিরজীবন একটি টবের ভিতর পরে রেখে দিতে পারে। শুনতে পাই, এইসব বামন-বট হচ্ছে অক্ষয়বট’। জাপানিদের বিশ্বাস যে, গাছকে হ্রস্ব করলে তা আর বন্ধ হয় না। সম্ভবত আমাদেরও মনুষ্যত্বের চর্চা সম্বন্ধে এই জাপানি আট জানা আছে, এবং বাল্যবিবাহ হচ্ছে সেই আর্টের একটি প্রধান অঙ্গ। এবং উক্ত কারণেই, অপরসকল প্রাচীন সমাজ উৎসন্নে গেলেও আমাদের সমাজ আজও টিকে আছে। মনুষ্যত্ব খর্ব করে মানবসমাজটাকে টবে জিইয়ে রাখায় যে বিশেষ-কিছু অহংকার করবার আছে, তা আমার মনে হয় না। সে যাই হোক, এ যুগে যখন কেউ যৌবনকে রাজটিকা দেবার প্রস্তাব করেন, তখন তিনি সমাজের কথা ভাবেন, ব্যক্তিবিশেষের কথা নয়।
ব্যক্তিগত হিসেবে জীবন ও যৌবন অনিত্য হলেও মানবসমাজের হিসেবে ও দুই পদার্থ নিত্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং সামাজিক জীবনে যৌবনের প্রতিষ্ঠা করা মানুষের ক্ষমতার বহির্ভূত না হলেও না হতে পারে।
কি উপায়ে যৌবনকে সমাজের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করা যেতে পারে, তাই হচ্ছে বিবেচ্য ও বিচার্য।
এ বিচার করবার সময় এ কথাটি মনে রাখা আবশ্যক যে, মানবজীবনের পর্ণ অভিব্যক্তি–যৌবন।
যৌবনে মানুষের বাহ্যেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় সব সজাগ ও সবল হয়ে ওঠে, এবং সৃষ্টির মূলে যে প্রেরণা আছে, মানুষে সেই প্রেরণা তার সকল অগে, সকল মনে অনুভব করে।
দেহ ও মনের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের উপর মানবজীবন প্রতিষ্ঠিত হলেও হেমনের পার্থক্যের উপরেই আমাদের চিন্তারাজ্য প্রতিষ্ঠিত। দেহের যৌবনের সঙ্গে মনের যৌবনের একটা যোগাযোগ থাকলেও দৈহিক যৌবন ও মানসিক যৌবন স্বতন্ত্র। এই মানসিক যৌবন লাভ করতে পারলেই আমরা তা সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে পারব। দেহ সংকীর্ণ ও পরিচ্ছিন্ন; মন উদার ও ব্যাপক। একের দেহের যৌবন অপরের দেহে প্রবেশ করিয়ে দেবার জো নেই; কিন্তু একের মনের যৌবন লক্ষ লোকের মনে সংক্রমণ করে দেওয়া যেতে পারে।
পূর্বে বলেছি যে, দেহ ও মনের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। একমাত্র প্রাণশক্তিই জড় ও চৈতন্যের যোগ সাধন করে। যেখানে প্রাণ নেই, সেখানে জড়ে ও চৈতন্যে মিলনও দেখা যায় না। প্রাণই আমাদের দেহ ও মনের মধ্যে মধ্যস্থতা করছে। প্রাণের পায়ের নীচে হচ্ছে জড়জগৎ, আর তার মাথার উপরে মনোজগৎ। প্রাণের ধর্ম যে, জীবনপ্রবাহ রক্ষা করা, নবনব সৃষ্টির দ্বারা সৃষ্টি রক্ষা করা— এটি সর্বলোকবিদিত। কিন্তু প্রাণের আর-একটি বিশেষ ধর্ম আছে, যা সকলের কাছে সমান প্রত্যক্ষ নয়। সেটি হচ্ছে এই যে, প্রাণ প্রতিমুহূর্তে রুপান্তরিত হয়। হিন্দুদর্শনের মতে, জীবের প্রাণময় কোষ, অন্নময় কোষ ও মনোময় কোষের মধ্যে অবস্থিত। প্রাণের গতি উভয়মুখী। প্রাণের পক্ষে মনোময় কোষে ওঠা এবং অন্নময় কোষে নামা দুই সম্ভব। প্রাণ অধোগতি প্রাপ্ত হয়ে জড়জগতের অন্তর্ভূত হয়ে যায়; আর উন্নত হয়ে মনোজগতের অন্তভূত হয়। মনকে প্রাণের পরিণতি এবং জড়কে প্রাণের বিকৃতি বললেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাণের স্বাভাবিক গতি হচ্ছে মনোজগতের দিকে; প্রাণের স্বাধীন ক্ষতিতে বাধা দিলেই তা জড়তাপ্রাপ্ত হয়। প্রাণ নিজের অভিব্যক্তির নিয়ম নিজে গড়ে নেয়; বাইরের নিয়মে তাকে বন্ধ করাতেই সে জড়জগতের অধীন হয়ে পড়ে। যেমন প্রাণীজগতের রক্ষার জন্য নিত্য নূতন প্রাণের সৃষ্টি আবশ্যক, এবং সে সৃষ্টির জন্য দেহের যৌবন চাই; তেমনি মনোজগতের এবং তদধীন কর্মজগতের রক্ষার জন্য সেখানেও নিত্য নব সৃষ্টির আবশ্যক, এবং সে সৃষ্টির জন্য মনের যৌবন চাই। পুরাতনকে আঁকড়ে থাকাই বার্ধক্য অর্থাৎ জড়তা। মানসিক যৌবন লাভের জন্য প্রথম আবশ্যক, প্রাণশক্তি যে দৈবী শক্তি— এই বিশ্বাস।
এই মানসিক যৌবনই সমাজে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য। এবং কি উপায়ে তা সাধিত হতে পারে, তাই হচ্ছে আলোচ্য।
আমরা সমগ্র সমাজকে একটি ব্যক্তিহিসেবে দেখলেও আসলে মানবসমাজ হচ্ছে বহব্যক্তির সমষ্টি। যে সমাজে বহু ব্যক্তির মানসিক যৌবন আছে, সেই সমাজেরই যৌবন আছে। দেহের যৌবনের সঙ্গেসঙ্গেই মনের যৌবনের আবির্ভাব হয়। সেই মানসিক যৌবনকে, স্থায়ী করতে হলে শৈশব নয়, বাধক্যের দেশ আক্রমণ এবং অধিকার করতে হয়। দেহের যৌবনের অন্তে বার্ধক্যের রাজ্যে যৌবনের অধিকার বিস্তার করবার শক্তি আমরা সমাজ হতেই সংগ্রহ করতে পারি। ব্যক্তিগত জীবনে ফাগন একবার চলে গেলে আবার ফিরে আসে না; কিন্তু সমগ্র সমাজে ফাগুনে চিরদিন বিরাজ করছে। সমাজে নূতন প্রাণ, নূতন মন, নিত্য জন্মলাভ করছে। অর্থাৎ নূতন সুখদুঃখ, নূতন আশা, নূতন ভালোবাসা, নূতন কর্তব্য ও নূতন চিন্তা নিত্য উদয় হচ্ছে। সমগ্র সমাজের এই জীবনপ্রবাহ যিনি নিজের অন্তরে টেনে নিতে পারবেন, তাঁর মনের যৌবনের আর ক্ষয়ের আশঙ্কা নেই। এবং তিনিই আবার কথায়। ও কাজে সেই যৌবন সমাজকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন।
এ যৌবনের কপালে রাজটিকা দিতে আপত্তি করবেন, এক জড়বাদী আর এক মায়াবাদী; কারণ এরা উভয়েই একমন। এরা উভয়েই বিশ্ব হতে অস্থির প্রাণটুকু বার করে দিয়ে যে এক স্থিরতত্ত্ব লাভ করেন, তাকে জড়ই বল আর চৈতন্যই বল, সে বস্তু হচ্ছে এক, প্রভেদ যা তা নামে।
জ্যৈষ্ঠ ১৩২১
রূপের কথা
এদেশে সচরাচর লোকে যা লেখে ও ছাপায় তাই যদি তাদের মনের কথা হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, আমরা মানবসভ্যতার চরম পদ লাভ করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এই প্রকাণ্ড সত্যটা বিদেশীরা মোটেই দেখতে পায় না। এটা সত্যিই দুঃখের বিষয়। কেননা, সভ্যতারও একটা চেহারা আছে; এবং যে সমাজের সচেহারা নেই, তাকে সুসভ্য বলে মানা কঠিন। বিদেশী বলতে দু শ্রেণীর লোক বোঝায়— এক পরদেশী, আর-এক বিলেতি। আমরা যে বড়-একটা কারও চোখে পড়ি নে, সেবিষয়ে এই দুই দলের বিদেশীই একমত।
যাঁরা কালাপানি পার হয়ে আসেন, তাঁরা বলেন যে, আমাদের দেশ দেখে তাঁদের চোখ জড়োয়, কিন্তু আমাদের বেশ দেখে সে চোখ ক্ষম হয়। এর কারণ, আমাদের দেশের মোড়কে রং আছে, আমাদের দেহের মোড়কে নেই। প্রকৃতি বাংলাদেশকে যে কাপড় পরিয়েছেন, তার রং সবুজ; আর বাঙালি নিজে যে কাপড় পরেছে, তার রং, আর যেখানেই পাওয়া যাক, ইন্দ্রধনুর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমরা আপাদমস্তক রং-ছট বলেই অপর কারও নয়নাভিরাম নই। সুতরাং যারা আমাদের দেশ দেখতে আসে, তারা আমাদের দেখে খুশি হয় না। যাঁর বোম্বাই-শহরের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় আছে, তিনিই জানেন কলকাতার সঙ্গে সে শহরের প্রভেদটা কোথায় এবং কত জাজল্যমান। সেদেশে জনসাধারণ পথেঘাটে সকালসন্ধ্যে রঙের ঢেউ খেলিয়ে যায় এবং সে রঙের বৈচিত্র্যের ও সৌন্দর্যের আর অন্ত নেই। কিন্তু আমাদের গায়ে জড়িয়ে আছে চির-গোধুলি; তাই শুধু বিলেতি নয়, পরদেশী ভারতবাসীর চোখেও আমরা এতটা দৃষ্টিকট। বাকি ভারতবর্ষ সাজসজ্জায় স্বদেশী, আমরা আধ-স্বদেশী হাফ-বিলেতি। আর বিলেতি মতে, হয় কালো নয় শাদা–নইলে সভ্যতার লজ্জা নিবারণ হয় না। রং চাই শুধু সং সাজবার জন্যে। আমাদের নবসভ্যতাও কার্যত এই মতে সায় দিয়েছে।
২.
আপনারা বলতে পারেন যে, একথা যদি সত্যও হয়, তাতে আমাদের কি যায়-আসে। বিদেশীর মনোরঞ্জন করবার জন্য আমরা তো আর জাতকে-জাত আমাদের পরন-পরিচ্ছদ আমাদের হাল-চাল সব বদলে ফেলতে পারি নে? জীবনযাত্রা ব্যাপারটা তো আর অভিনয় নয় যে, দর্শকের মুখ চেয়ে সে-জীবন গড়তে হবে এবং তার উপর আবার রং ফলাতে হবে। একথা খুব ঠিক। জীবন আমরা কিসের জন্য ধারণ করি তা না জানলেও, এটা জানি যে, পরের জন্য আমরা তা ধারণ করি নে–অপর দেশের অপর লোকের জন্য তো নয়ই। তবে বিদেশীর কথা উত্থাপন করবার সার্থকতা এই যে, জাতীয়জীবনের একটি বিদেশীর চোখে যেমন একনজরে ধরা পড়ে, স্বদেশীর চোখে তা পড়ে না। কেননা, আজন্ম দেখে দেখে লোকের চোখে যা সয়ে গেছে, যারা প্রথম দেখে তাদের চোখে তা সয় না।
এই বিদেশীরাই আমাদের সজ্ঞান করে দিয়েছে যে, রূপ সম্বন্ধে আমরা চোখ থাকতেও কানা। আমাদের রূপজ্ঞান যে নেই, কিংবা যদি থাকে তো অতি কম, সেবিষয়ে বোধ হয় কোনো মতভেদ নেই। কেননা, এ জ্ঞানের অভাবটা আমরা জাতীয় মনের দৈন্য বলে মনে করি নে। বরং সত্যকথা বলতে গেলে, আমাদের বিশ্বাস যে, এই রূপান্ধতাটাই আমাদের জাতীয় চরিত্রের মহত্ত্বের পরিচয় দেয়। রূপ তো একটা বাইরের জিনিস; শুধু তাই নয়, বাহ্যবস্তুরও বাইরের জিনিস; ও জিনিসকে যারা উপেক্ষা, এমনকি অবজ্ঞা, করতে না শিখেছে তারা আধ্যাত্মিকতার সন্ধান জানে না। আর আমরা আরকিছু হই আর না-হই, বালবৃদ্ধবনিতা সকলেই যে আধ্যাত্মিক। সেকথা যে অস্বীকার করবে, সে নিশ্চয়ই স্বদেশ এবং স্বজাতিদ্রোহী।
৩.
রপ-জিনিসটাকে যাঁরা একটা পাপ মনে করেন, তাঁদের মতে অবশ্য রুপের প্রশ্রয় দেওয়ার অর্থ পাপের প্রশ্রয় দেওয়া। কিন্তু দলে পাতলা হলেও পৃথিবীতে এমনসব লোক আছে, যারা রূপকে মান্য করে শ্রদ্ধা করে, এমনকি পুজো করতেও প্রস্তুত; অথচ নিজেদের মহাপাপী মনে করে না। এই রূপেভক্তের দল অবশ্য স্বদেশীর কাছে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য, অর্থাৎ প্রমাণপ্রয়োগ-সহকারে রুপের স্বত্বসাব্যস্ত করতে বাধ্য। আপসোসের কথা এই যে, যে সত্য সকলের প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত, সেই সত্য এদেশে প্রমাণ করতে হয়— অর্থাৎ একটা সহজ কথা বলতে গেলে, আমাদের ন্যায়-অন্যায়ের স্রোতের উজান ঠেলে যেতে হয়।
যা সকলে জানে–আছে, তা নেই বলাতে অতিবন্ধির পরিচয় দেওয়া হতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা এই ‘অতি’র অতিভক্ত হওয়াতে আমাদের ইতির জ্ঞান নষ্ট হয়েছে।
বস্তুর রূপে বলে যে একটি ধর্ম আছে, এ হচ্ছে শোনা-কথা নয়। দেখাজিনিস। যাঁর চোখ-নামক ইন্দ্রিয় আছে, তিনিই কখনো-না-কখনো তার সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। এবং আমাদের সকলেরই চোখ আছে; সম্ভবত শুধু তাঁদের ছাড়া, যাঁরা সৌন্দর্যের নাম করলেই অতীন্দ্রিয়তার ব্যাখ্যান অর্থাৎ উপাখ্যান শর, করেন। কিন্তু আমি এই রূপ-জিনিসটিকে অতিবজিত ইন্দ্রিয়ের কোঠাতেই টিকিয়ে রাখতে চাই; কেননা, অতীন্দ্রিয়-জগতে রূপ নিশ্চয়ই অরূপ হয়ে যায়।
৪.
রূপের বিষয় দার্শনিকেরা কি বলেন আর না-বলেন, তাতে কিছু যায়আসে না; কেননা, যা দৃষ্টির অগোচর, তাই দর্শনের বিষয়। অতএব একথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, বস্তুর রূপ বলে যে একটি গুণ আছে, তা মানুষমাত্রেই জানে এবং মানে। তবে সেই গুণের পক্ষপাতী হওয়াটা গুণের কি দোষের— এই নিয়েই যা মতভেদ।
রূপকে আমরা ভক্তি করি নে, সম্ভবত ভালোবাসি নে। আপনারা সকলেই জানেন যে, হালে একটা মতের বহুলপ্রচার হয়েছে, যার ভিতরকার কথা এই যে, জাতীয় আত্মমর্যাদা হচ্ছে পরশ্রীকাতরতারই সদর পিঠ। সম্ভবত একথা সত্য, কিন্তু তাই বলে শ্রীকাতরতাও যে ঐ জাতীয় আত্মমর্যাদার লক্ষণ একথা স্বীকার করা যায় না; কেননা, বিশ্বমানবের সভ্যতার ইতিহাস এর বিরদ্ধে চিরদিন সাক্ষি দিয়ে আসছে।
স্বদেশের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলেই অপর সভ্যজাতির কাছে রূপের মর্যাদা যে কত বেশি, তার প্রমাণ হাতে-হাতে পাওয়া যাবে। বর্তমান ইউরোপ সুন্দরকে সত্যের চাইতে নীচে আসন দেয় না, সেদেশে জ্ঞানীর চাইতে আর্টিস্টের মান্য কম নয়। তারা সভ্যসমাজের দেহটাকে অর্থাৎ দেশের রাস্তাঘাট বাড়িঘরদোর মন্দিরপ্রাসাদ, মানুষের আসনবসন সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি নিত্য নূতন করে সুন্দর করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করছে। সে চেষ্টার ফল স, কি কু হচ্ছে, সে স্বতন্ত্র কথা। ইউরোপীয় সভ্যতার ভিতর অবশ্য একটা কুৎসিত দিক আছে, যার নাম কমার্শিয়ালিজম; কিন্তু এই দিকটে কদর্য বলেই তার সর্বনাশের দিক। কমার্শিয়ালিজম,এর মূলে আছে লোভ। আর লোভে পাপ পাপে মৃত্যু। আপনারা সকলেই জানেন যে, রূপের সঙ্গে মোহের সম্পর্ক থাকতে পারে, কিন্তু লোভের নেই।
ইউরোপ ছেড়ে এশিয়াতে এলে দেখতে পাই যে, চীন ও জাপান রূপের এতই ভক্ত যে, রুপের আরাধনাই সেদেশের প্রকৃত ধর্ম বললেও অত্যুক্তি হয় না। রূপের প্রতি এই পরাপ্ৰীতিবশত চীনজাপানের লোকের হাতে-গড়া এমন জিনিস নেই যার রূপ নেই–তা সে ঘটিই হোক আর বাটিই হোক। যাঁরা তাদের হাতের কাজ দেখেছেন, তাঁরাই তাদের রূপ-সৃষ্টির কৌশল দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছেন। মোঙ্গলজাতিকে ভগবান রূপ দেন নি, সম্ভবত সেই কারণে সন্দরকে তাদের নিজের হাতে গড়ে নিতে হয়েছে। এই তো গেল বিদেশের কথা।
৫.
আবার শুধু স্বদেশের নয়, সকালের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেলে আমরা ঐ একই সত্যের পরিচয় পাই। প্রাচীন গ্রীকো-ইতালীয় সভ্যতার ঐকান্তিক রূপচর্চার ইতিহাস তো জগৎবিখ্যাত। প্রাচীন ভারতবর্ষও রূপ সম্বন্ধে অন্ধ ছিল না; কেননা, আমরা যাই বলি নে কেন, সে সভ্যতাও মানবসভ্যতা–একটা সৃষ্টিছাড়া পদার্থ নয়। সে সভ্যতারও শুধু আত্মা নয়, দেহ ছিল; এবং সে দেহকে আমাদের পপুরুষেরা সুঠাম ও সুন্দর করেই গড়তে চেষ্টা করেছিলেন। সে দেহ আমাদের চোখের সম্মুখে নেই বলেই আমরা মনে করি যে, সেকালে যা ছিল তা হচ্ছে শুধু অশরীরী আত্মা। কিন্তু সংস্কৃতসাহিত্য থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাঁদের কতটা সৌন্দর্য জ্ঞান ছিল। আমরা যাকে সংস্কৃতকাব্য বলি, তাতে রূপবর্ণনা ছাড়া আর বড়-কিছু নেই; আর সে রূপবর্ণনাও আসলে দেহের, বিশেষত রমণী-দেহের, বর্ণনা; কেননা, সে কাব্যসাহিত্যে যে প্রকৃতিবর্ণনা আছে তাও বস্তুত রমণীর রূপবর্ণনা। প্রকৃতিকে তাঁরা সুন্দরী রমণী হিসেবেই দেখেছিলেন। তার যে অংশ নারীঅঙ্গের উপমেয় কি উপমান নয়, তার স্বরূপ হয় তাঁদের চোখে পড়ে নি, নয় তা তাঁরা রূপ বলে গ্রাহ্য করেন নি। সংস্কৃতসাহিত্যে হরেকরকমের ছবি আছে, কিন্তু ল্যাণ্ডসকেপ নেই বললেই হয়; অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক প্রকৃতির অস্তিত্বের বিষয় তাঁরা সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। ল্যাণ্ডসকেপ প্রাচীন গ্রীস কিংবা রোমের হাত থেকেও বেরয় নি। তার কারণ, সেকালে মানুষে মানুষে বাদ দিয়ে বিশ্বসংসার দেখতে শেখে নি। এর প্রমাণ শুধু আটে নয়, দর্শনে-বিজ্ঞানেও পাওয়া যায়। আমরা আমাদের নববিজ্ঞানের প্রসাদে মানুষকে এ বিশ্বের পরমাণুতে পরিণত করেছি, সম্ভবত সেই কারণে আমরা মানবদেহের সৌন্দর্য অবজ্ঞা করতে শিখেছি। আমাদের পূর্বপুরুষেরা কিন্তু সে সৌন্দর্যকে একটি অমূল্য বস্তু বলে মনে করতেন; শুধু স্ত্রীলোকের নয়, পুরুষের রূপের উপরও তাঁদের ভক্তি ছিল। যাঁর অলোকমান্য রূপ নেই, তাঁকে এদেশে পুরাকালে মহাপুরুষ বলে কেউ মেনে নেয় নি। শ্রীরামচন্দ্র বুদ্ধদেব শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারেরা সকলেই সৌন্দর্যের অবতার ছিলেন। রূপগণের সন্ধিবিচ্ছেদ করা সেকালের শিক্ষার একটা প্রধান অঙ্গ ছিল না। শুধু তাই নয়, আমাদের পূর্বপুরুষদের কদাকারের উপর এতটাই ঘণা ছিল যে, পরাকালের শদ্রেরা যে দাসত্ব হতে মুক্তি পায় নি, তার একটি প্রধান কারণ তারা ছিল কৃষ্ণবর্ণ এবং কুৎসিত অন্তত আর্যদের চোখে। সেকালের দর্শনের ভিতর অরূপের জ্ঞানের কথা থাকলেও সেকালের ধর্ম রূপজ্ঞানের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। পরব্রহ নিরাকার হলেও ভগবান, মন্দিরে মন্দিরে মতিমান। প্রাচীন মতে নির্গুণ-ব্রহ্ম অরূপ এবং সগুণ-ব্রহ্ম স্বরূপ।
৬.
সভ্যতার সঙ্গে সৌন্দর্যের এই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকবার কারণ, সভ্যসমাজ বলতে বোঝায় গঠিত-সমাজ। যে সমাজের গড়ন নেই, তাকে আমরা সভ্যসমাজ বলি নে। একালের ভাষায় বলতে হলে সমাজ হচ্ছে একটি অর্গানিজম; আর আপনারা সকলেই জানেন যে সকল অর্গানিজম, একজাতীয় নয়, ও-বস্তুর ভিতর উচুনিচুর প্রভেদ বিস্তর। অর্গানিক-জগতে প্রোটোপ্ল্যাজম হচ্ছে সবচাইতে নীচে এবং মানুষ সবচাইতে উপরে। এবং মানুষের সঙ্গে প্রোটোপ্ল্যাজম এর প্রত্যক্ষ পার্থক্য হচ্ছে রূপে; অপর-কোনো প্রভেদ আছে কি না, সে হচ্ছে তর্কের বিষয়। মানুষে যে প্রোটোপ্ল্যাজম,এর চাইতে রূপবান, এবিষয়ে, আশা করি, কোনো মতভেদ নেই। এই থেকে প্রমাণ হয় যে, যে সমাজের চেহারা যত সুন্দর, সে সমাজ তত সভ্য। এরূপ হবার একটি স্পষ্ট কারণও আছে। এ জগতে রূপ হচ্ছে শক্তির চরম বিকাশ; সমাজ গড়বার জন্য মানুষের শক্তি চাই এবং সুন্দর করে গড়বার জন্য তার চাইতেও বেশি শক্তি চাই। সুতরাং মানুষ যেমন বাড়বার মুখে ক্ৰমে অধিক সশ্রী হয়ে ওঠে এবং মরবার মুখে ক্রমে অধিক কুশ্রী হয় জাতের পক্ষেও সেই একই নিয়ম খাটে। কদর্যতা দুর্বলতার বাহ্য লক্ষণ, সৌন্দর্য শক্তির। এই ভারতবর্ষের অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যায় যে, যখনই দেশে নবশক্তির আবির্ভাব হয়েছে তখনই মঠে-মন্দিরে-বেশে-ভূষায় মানুষের আশায়-ভাষায় নবসৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। ভারতবর্ষের আর্টের বৌদ্ধযুগ ও বৈষ্ণবযুগ এই সত্যেরই জাজল্যমান প্রমাণ।
আমাদের এই কোণঠাসা দেশে যেদিন চৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়, সেইদিনই বাঙালি সৌন্দর্যের আবিষ্কার করে। এর পরিচয় বৈষ্ণবসাহিত্যে পাওয়া যায়। কিন্তু সে সৌন্দর্যবৃদ্ধি যে টিকল না, বাংলার ঘরেবাইরে যে তা নানারূপে নানা আকারে ফটল না তার কারণ চৈতন্যদেব যা দান করতে এসেছিলেন তা ষোলোআনা গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের ছিল না। যে কারণে বাংলার বৈষ্ণবধর্ম বাঙালিসমাজকে একাকার করবার চেষ্টায় বিফল হয়েছে, হয়ত সেই একই কারণে তা বাঙালিসভ্যতাকে সাকার করে তুলতে পারে নি। ভক্তির রস আমাদের বুকে ও মুখে গড়িয়েছে, আমাদের মনে ও হাতে তা জমে নি। ফলে, এক গান ছাড়া আর-কিছুকেই আমরা নবরপ দিতে পারি নি।
৭.
এসব কথা যদি সত্য হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের রূপজ্ঞানের অভাবটা আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেয় না। কিন্তু একথা মুখ ফটে বললেই আমাদের দেশের অন্ধের দল লগড় ধারণ করবেন। এর কারণ কি, তা বলছি।
সত্য ও সৌন্দর্য, এ দুটি জিনিসকে কেউ উপেক্ষা করতে পারেন না। হয় এদের ভক্তি করতে হবে, নয় অভক্তি করতে হবে। অর্থাৎ সত্যকে উপেক্ষা করলে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে; আর সুন্দরকে অবজ্ঞা করলে কুৎসিতের প্রশ্রয় দিতেই হবে। এ পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত এক স, আর-এক কু। সু-কে অর্জন না করলে কু-কে বর্জন করা কঠিন। আমাদের দশাও হয়েছে তাই। আমাদের সুন্দরের প্রতি যে অনুরাগ নেই, শুধু তাই নয়, ঘোরতর বিরাগ আছে।
আমরা দিনে-দুপুরে চীৎকার করে বলি যে, সাহিত্যে যে ফলের কথা জ্যোৎস্নার কথা লেখে সে লেখক নিতান্তই অপদার্থ।
এঁদের কথা শুনলে মনে হয় যে, সব ফলই যদি ডুমুর হয়ে ওঠে আর অমাবস্যা যদি বারোমেসে হয়, তাহলেই এ পৃথিবী ভূস্বর্গ হয়ে উঠবে; এবং সে স্বর্গে অবশ্য কোনো কবির স্থান হবে না। চন্দ্র যে সৌরমণ্ডলের মধ্যে একটি প্রক্ষিপ্ত গোলক, সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ও রিফ্লেক্টর ভগবান আকাশে ঝুলিয়ে দিয়েছেন; সুতরাং জ্যোৎস্না যে আছে, তার জন্য কবি দায়ী নন, দায়ী স্বয়ং ভগবান। কিন্তু এই জ্যোৎস্নাবিদ্বেষ থেকেই এদের প্রকৃত মনোভাব বোঝা যায়। এ রাগটা আসলে আলোর উপর রাগ। জ্ঞানের আলোক যখন আমাদের চোখে পরোপরি সয় না, তখন রূপের আলোক যে মোটেই সইবে না— তাতে আর বিচিত্র কি। জ্ঞানের আলো বস্তুজগৎকে প্রকাশ করে, সুতরাং এমন অনেক বস্তু প্রকাশ করে, যা আমাদের পেটের ও প্রাণের খোরাক যোগাতে পারে; কিন্তু রুপের আলো শুধু নিজেকেই প্রকাশ করে, সুতরাং তা হচ্ছে শুধু আমাদের চোখের ও মনের খোরাক। বলা বাহুল্য, উদর ও প্রাণ প্রোটোল্যাজম এরও আছে, কিন্তু চোখ ও মন শুধু মানুষেরই আছে। সুতরাং যাঁরা জীবনের অর্থ বোঝেন একমাত্র বেচে থাকা এবং তজ্জন্য উদরপতি করা, তাঁদের কাছে জ্ঞানের আলো গ্রাহ্য হলেও রূপের আলো অবজ্ঞাত। এ দুয়ের ভিতর প্রভেদও বিস্তর। জ্ঞানের আলো শাদা ও একঘেয়ে, অর্থাৎ ও হচ্ছে আলোর মূল; অপরপক্ষে, রূপের আলো রঙিন ও বিচিত্র, অর্থাৎ আলোর ফল। আদিম মানবের কাছে ফলের কোনো আদর নেই, কেননা ও-বস্তু আমাদের কোনো আদিম ক্ষুধার নিবৃত্তি করে না; ফলে আর-যাই হোক, চর্ব্য-চোষ্য কিংবা লেহ্য-পেয় নয়।
৮.
এসব কথা শুনে আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুরা নিশ্চয়ই বলবেন যে, আমি যা বলছি সেসব জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা নয়, সেরেফ কবিত্ব। বিজ্ঞানের কথা এই যে, যে আলোকে আমি শাদা বলছি, সেই হচ্ছে এ বিশ্বের একমাত্র অখণ্ড আলো; সেই সমস্ত আলো রিফ্র্যাকটেড অর্থাৎ ব্যস্ত হয়েই আমাদের চোখে বহুরুপী হয়ে দাঁড়ায়। তথাস্তু। এই রিফ্র্যাকশনএর একাধারে নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ হচ্ছে–পঞ্চভূতের বহির্ভূত ইথার-নামক রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শশব্দের অতিরিক্ত একটি পদার্থ। এবং এই হিল্লোলিত পদার্থের ধর্ম হচ্ছে এই জড়জগৎটাকে উৎফুল্ল করা, রুপান্বিত করা। রূপ যে আমাদের খুল-শরীরের কাজে লাগে না, তার কারণ বিশ্বের স্থূল-শরীর থেকে তার উৎপত্তি হয় নি। আমাদের ভিতর যে সক্ষম-শরীর অর্থাৎ ইথার আছে, বাইরের রূপের স্পর্শে সেই সুক্ষ-শরীর স্পন্দিত হয়, আনন্দিত হয়, পুলকিত হয়, প্রস্ফুটিত হয়। রূপজ্ঞানেই মানুষের জীবন্মক্তি, অর্থাৎ স্থূল-শরীরের বন্ধন হতে মুক্তি। রূপজ্ঞান হারালে মানুষ আজীবন পঞ্চভূতেরই দাসত্ব করবে। রূপবিদ্বেষটা হচ্ছে আত্মার প্রতি দেহের বিদ্বেষ, আলোর বিরুদ্ধে অন্ধকারের বিদ্রোহ। রূপের গুণে অবিশ্বাস করাটা নাস্তিকতার প্রথম সত্র।
৯.
ইন্দ্ৰিয়জ বলে বাইরের রূপের দিকে পিঠ ফেরালে ভিতরের রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন; কেননা, ইন্দ্রিয়ই হচ্ছে জড় ও চৈতন্যের একমাত্র বন্ধনসত্র। এবং ঐ সত্রেই রূপের জন্ম। অন্তরের রূপও যে আমাদের সকলের মনশ্চক্ষে ধরা পড়ে না, তার প্রমাণস্বরূপ একটা চলতি উদাহরণ নেওয়া যাক।
রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রতি অনেকের বিরক্তির কারণ এই যে, সে লেখার রূপ আছে। রবীন্দ্রনাথের অন্তরে ইথার আছে, তাই সে মনের ভিতর দিয়ে যে ভাবের আলো রিফ্র্যাকটেড হয়ে আসে, তা ইন্দ্রধনুর বর্ণে রঞ্জিত ও ছন্দে মত হয়ে আসতে বাধ্য। স্থূলদর্শীর স্থূলষ্টিতে তা হয় অসত্য নয় অশিব বলে ঠেকা কিছু আশ্চর্য নয়।
মানুষে তিনটি কথাকে বড় বলে স্বীকার করে, তার অর্থ তারা বুঝুক আর না- বুঝুক। সে তিনটি হচ্ছে : সত্য শিব আর সুন্দর। যার রুপের প্রতি বিদ্বেষ আছে, সে সন্দরকে তাড়না করতে হলে হয় সত্যের নয় শিবের দোহাই দেয়; যদিচ সম্ভবত সে ব্যক্তি সত্য কিংবা শিবের কখনো একমনে সেবা করে নি। যদি কেউ বলেন যে, সুন্দরের সাধনা কর— অমনি দশজনে বলে ওঠেন, কি দ-নীতির কথা। বিষয়বধির মতে সৌন্দর্যপ্রিয়তা বিলাসিতা এবং রূপের চচা চরিত্রহীনতার পরিচয় দেয়। সন্দরের উপর এদেশে সত্যের অত্যাচার কম, কেননা এদেশে সত্যের আরাধনা করবার লোকও কম। শিবই হচ্ছে এখন আমাদের একমাত্র, কেননা অমনি-পাওয়া, ধন। এ তিনটির প্রতিটি যে প্রতিঅপরটির শত্র, তার কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং এদের একের প্রতি অভক্তি অপরের প্রতি ভক্তির পরিচায়ক নয়। সে যাই হোক, শিবের দোহাই দিয়ে কেউ কখনো সত্যকে চেপে রাখতে পারে নি; আমার বিশ্বাস, সুন্দরকেও পারবে না। যে জানে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, সে সে-সত্য স্বীকার করতে বাধ্য, এবং সামাজিক জীবনের উপর তার কি ফলাফল হবে সেকথা উপেক্ষা করে সে-সত্য প্রচার করতেও বাধ্য। কেননা, সত্যসেবকদের একটা বিশ্বাস আছে যে, সত্যজ্ঞানের শেষফল ভালো বই মন্দ নয়। তেমনি যার রূপজ্ঞান আছে, সে সৌন্দর্যের চর্চা এবং সুন্দর বস্তুর সৃষ্টি করতে বাধ্য তার আশু সামাজিক ফলাফল উপেক্ষা করে, কেননা রুপের পূজারীদেরও বিশ্বাস যে, রূপজ্ঞানের শেষফল ভালো বই মন্দ নয়। তবে মানুষের এ জ্ঞানলাভ করতে দেরি লাগে।
শিবজ্ঞান আসে সবচাইতে আগে। কেননা, মোটামুটি ও-জ্ঞান না থাকলে সমাজের সৃষ্টিই হয় না, রক্ষা হওয়া তো দুরের কথা। ও জ্ঞান বিষয়বৃদ্ধির উত্তমাঙ্গ হলেও একটা অঙ্গমাত্র।
তার পর আসে সত্যের জ্ঞান। এ জ্ঞান শিবজ্ঞানের চাইতে ঢের সক্ষমজ্ঞান এবং এ জ্ঞান আংশিকভাবে বৈষয়িক, অতএব জীবনের সহায়; এবং আংশিকভাবে তার বহির্ভূত, অতএব মনের সম্পদ।
সবশেষে আসে রূপজ্ঞান। কেননা, এ জ্ঞান অতিসক্ষম এবং সাংসারিক হিসেবে অকেজো। রূপজ্ঞানের প্রসাদে মানুষের মনের পরমায়ু বেড়ে যায়, দেহের নয়। সুনীতি সভ্যসমাজের গোড়ার কথা হলেও সুরুচি তার শেষকথা। শিব সমাজের ভিত্তি, আর সুন্দর তার অভ্রভেদী চড়া।
অবশ্য হার্বার্ট স্পেনসার বলেছেন যে, মানুষের রূপজ্ঞান আসে আগে এবং সত্যজ্ঞান তার পরে। তার কারণ, যে জ্ঞান তাঁর জন্মায় নি, তিনি মনে করতেন সে জ্ঞান বাতিল হয়ে গিয়েছে। সত্যকথা এই যে, মানবসমাজের পক্ষে রূপজ্ঞান লাভ করাই সাধনাসাপেক্ষ খোয়ানো সহজ। আমাদের পর্বপুরুষদের সাধনার সেই বঞ্চিত ধন আমরা অবহেলাক্রমে হারিয়ে বসেছি। বিলেতি সভ্যতার কেজো অংশের সংস্পর্শে আমাদের মনের ভিত টলকে আর না-টলুক, তার চড়া ভেঙে পড়েছে।
এবিষয়ে বৌদ্ধদর্শনের মত প্রণিধানযোগ্য। বৌদ্ধদার্শনিকেরা কল্পনা করেন যে, এ জগতে নানা লোক আছে। সবনীচে কামলোক, তার উপরে রূপলোক, তার উপরে ধ্যানলোক ইত্যাদি।
আমার ধারণা, আমরা-সব জন্মত কামলোকের অধিবাসী; সুতরাং রূপলোকে যাওয়ার অর্থ আত্মার পক্ষে ওঠা, নামা নয়।
আর-এক কথা, রূপের চর্চার বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, আমরা দরিদ্র জাতি–অতএব ও আমাদের সাধনার ধন নয়। এ ধারণার কারণ, ইউরোপের কমার্শিয়ালিজম, আমাদের মনের উপর এ যুগে রাজার মত প্রভুত্ব করছে। সত্যকথা এই যে, জাতীয়-শ্রীহীনতার কারণ অর্থের অভাব নয়, মনের দারিদ্র। তার প্রমাণ, আমাদের হালফ্যাশানের বেশভূষা সাজসজ্জা আচারঅনুষ্ঠানের শ্রীহীনতা সোনার-জলে ছাপানো বিয়ের কবিতার মত আমাদের ধনীসমাজেই বিশেষ করে ফুটে উঠেছে। আসল কথা, আমাদের নবশিক্ষার বৈজ্ঞানিক আলোক আমাদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করুক আর নাই করুক, আমাদের রূপেকানা করেছে। গুণ হয়ে দোষ হল বিদ্যার বিদ্যায়’–ভারতচন্দ্রের একথা সুন্দরের দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে, আমাদের সকলের পক্ষেই সমান খাটে। আর যদি এইকথাই সত্য হয় যে, আমরা সুন্দরভাবে বাঁচতে পারি নে— তাহলে আমাদের সুন্দরভাবে মরাই শ্রেয়। তাতে পৃথিবীর কারও কোনো ক্ষতি হবে না, এমনকি আমাদেরও নয়।
ফাল্গুন ১৩২৩
শিক্ষার নব আদর্শ
শ্ৰীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যে এদেশের চলতি শিক্ষার দর যাচাই করতে উদ্যত হয়েছেন, এ অতি সুখের কথা। কেননা, বাঙালি যদি কোনো বস্তু লাভ করবার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তো সে হচ্ছে শিক্ষা। সুতরাং আমরা দেশস ভদ্রসন্তান প্রাণপাত করে যা পাই, জহরির কাছে তার মূল্য যে কি, তা জানায় ক্ষতি নেই।
আমরা যে কত শিক্ষালোভী, তার প্রমাণ আমাদের পাঁচ বৎসর বয়েসে হাতে-খড়ি হয়। আর কমসেকম একুশ বৎসর বয়েসে হাতে-কালি মুখে-কালি আমরা সেনেট-হাউস থেকে লিখে আসি। কিন্তু এতেও আমাদের শিক্ষার সাধ মেটে না। এর পরে আমরা সারাজীবন যখন যা-কিছু পড়ি–তা কবিতাই হোক আর গল্পই হোক; আমাদের মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, আমরা এ পড়ে কি শিক্ষা লাভ করলম। এ প্রশ্নের উত্তর মুখে-মুখে দেওয়া অসম্ভব; কেননা, সাহিত্যের যা শিক্ষা, তা হাতে-হাতে পাওয়া যায় না। সাহিত্য যা দেয়, তা আনন্দ; কিন্তু ও-বস্তু আমরা জানি নে বলে মানি নে। আমাদের শিক্ষার ভিতর আনন্দ নেই বলে আনন্দের ভিতর যে শিক্ষা থাকতে পারে, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।
ফলে, পাঠকমাত্রই যখন শিক্ষার্থী, তখন লেখকমাত্রকেই দায়ে-পড়ে শিক্ষক হতে হয়। পাঠকসমাজ যখন আমাদের কাছে শিক্ষা নিতে প্রস্তুত, তখন অবশ্য শিক্ষা দিতে আমাদের নারাজ হওয়া উচিত নয়; কেননা, লেকচারজিনিসটে দেওয়া সহজ, শোনাই কঠিন। তবে যে আমরা পাঠকদের সকল সময় শিক্ষা না দিয়ে সময়-সময় আনন্দ দেবার বৃথা চেষ্টা করে তাঁদের বিরাগভাজন হই, তার একটি বিশেষ কারণ আছে।
বাংলাসাহিত্যের যে শুধু পাঠক আছেন তা নয়, পাঠিকাও আছেন। দলে বোধ হয় উভয়েই সমান পরে হবেন, অথচ এ উভয়ের ভিতর বিদ্যার প্রভেদ বিস্তর। পাঠকেরা-সব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাত্তীর্ণ; পাঠিকারা বালিকাবিদ্যালয়ের পরীক্ষাত্তীর্ণও নন। সুতরাং পাঠকদের জন্য লেখকদের পোস্টগ্র্যাজুয়েট লেকচার দেওয়া কর্তব্য, এবং পাঠিকাদের জন্য নিম্ন-প্রাইমারির। অথচ শ্রোতাদের শিক্ষা দিতে হলে আমাদের পক্ষে সেইরূপ বক্তৃতা করা আবশ্যক যা সকলের পক্ষে সমান উপযোগী হয়। অসাধ্যসাধন করবার দুঃসাহস সকলের নেই, সম্ভবত সেই কারণে বাংলার কাব্যসাহিত্য শিক্ষাদানের ভার হাতে নেয় নি।
কিন্তু এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের পক্ষে সমান শিক্ষাপ্রদ সাহিত্য যে রচনা করা যায় না, এ ধারণা অমূলক। উপর-উপর দেখলেই এদেশের শিক্ষিত লোক এবং অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের বিদ্যাবুদ্ধির প্রভেদ মস্ত দেখায়; কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, আমরা মনে সকলেই এক। মনোরাজ্যে যে আমাদের লিঙ্গভেদ নেই, বর্ণভেদ নেই, বয়োভেদ নেই তার প্রমাণ হাতে-কলমে দেখানো যেতে পারে। ‘ঘরেবাইরে’ লেখবার কৈফিয়ত তলব করে একটি ভদ্রমহিলা রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখেছিলেন, তা যে-কোনো এম. এ. পাশ-করা প্রোফেসর লিখতে পারতেন, এবং উক্ত গল্প পাঠ করে একটি এম. এ. পাশকরা প্রোফেসরের মনে যে সমস্যার উদয় হয়েছে, তা যে-কোনো ভদ্রমহিলার মনে উদয় হতে পারত। অতএব যে-কোনো শিকারী সাহিত্যিক একটি বাক্যবাণে এ দুটি পাখিকেই বিদ্ধ করতে পারেন। বস্তুগত্যা আমাদের মন হচ্ছে হরীতকী-জাতীয়; শিক্ষার গুণে সে মন পাকে না, শুধু শুকিয়ে যায়। সুতরাং বাংলার অশিক্ষিত স্ত্রীলোক ও শিক্ষিত পুরুষ–এ দুয়ের মনের ভিতর প্রভেদ এই যে, এর একটি কাঁচা আর অপরটি শুকনো। দেশসুদ্ধ লোক সেই শিক্ষা চান, যে শিক্ষার গুণে স্ত্রীপুরুষ সকলের মন সমান শুকিয়ে ওঠে। কেননা, হরীতকী যত বেশি শকোয়, যত বেশি তিতো হয়, তত বেশি উপকারী হয়। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ সেই শিক্ষার সন্ধানে ফিরছেন, যে শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মন-হরীতকী পেকে উঠবে, এবং যার আস্বাদ গ্রহণ করে স্বজাতি অমরত্ব লাভ করবে। এক্ষেত্রে দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের মিল হবার কোনো সম্ভাবনা নেই; কেননা, উভয়ের আদশ সম্পূর্ণ বিভিন্ন।
আমাদের পক্ষে কি শিক্ষা ভালো, তা নির্ণয় করবার পূর্বে–আমরা কি হতে চাই, সেবিষয়ে মনঃস্থির করা আবশ্যক। কেননা, একটা স্পষ্ট জাতীয় আদশ না থাকলে, জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে না। ধরন, যদি অশ্বত্ব-লাভ-করা গর্দভদের জাতীয় আদর্শ করে তোলা যায়, তাহলে অবশ্য সে জাতির শিক্ষকেরাও তাদের জন্য পেটনের ব্যবস্থা করবেন; অপরপক্ষে গভত্ব লাভ করা যদি অন্যদের জাতীয় আদর্শ করে তোলা যায়, তাহলে সে জাতির শিক্ষকেরাও তাদের জন্য ঐ পেটনেরই ব্যবস্থা করবেন। হয় গাধা-পিটে-ঘোড়া, নয় ঘোড়া-পিটে-গাধা করাই যে শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য–সাধারণত এইটেই হচ্ছে লোকের ধারণা। এবং আমরা এই উভয়ের মধ্যে যে কোন, জাতীয়, সেবিষয়ে দেশে-বিদেশে বিষম মতভেদ থাকলেও পেটন দেওয়াটাই যে শিক্ষা দেবার একমাত্র পদ্ধতি, সেবিষয়ে বিশেষ কোনো মতভেদ নেই। কাজেই আমাদের শিক্ষকেরা এক হাতে সংস্কৃত, আর-এক হাতে ইংরেজি ধরে আমাদের উপর দ হাতে চাবুক চালাচ্ছেন। এর ফলে কত গাধা ঘোড়া এবং কত ঘোড়া গাধা হচ্ছে–তা বলা কঠিন; কেননা, এবিষয়ের কোনো স্ট্যাটিস্টিকস অদ্যাবধি সংগ্রহ করা হয় নি।
সে যাই হোক, যে জাতীয় আদর্শের উপর জাতীয় শিক্ষা নির্ভর করে, তা যুগপৎ মনের এবং জীবনের আদর্শ হওয়া দরকার। যেদেশে জাতীয় শিক্ষা আছে, সেদেশের প্রতি ঈষৎ দৃষ্টিপাত করলেই এ সত্য সকলের কাছেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। ইউরোপে আমরা দেখতে পাই যে, জর্মানি চেয়েছিল যা নই তাই হব’, ইংলণ্ড যা আছি তাই থাকব, আর ফ্রান্স যা আছি তাও থাকব না, যা নই তাও হব না; এবং এই তিন দেশের গত পঞ্চাশ বৎসরের কাজ ও কথার ভিতর নিজ-নিজ জাতীয় আদর্শের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে।
কিন্তু আমাদের বিশেষত্ব এই যে, আমরা জীবনে এক পথে চলতে চাই–মনে আর-এক পথে।
আমাদের ব্যক্তিগত মনের আদর্শ হচ্ছে ‘যা ছিলুম তাই হওয়া’, আর আমাদের জাতিগত জীবনের আদর্শ হচ্ছে ‘যা ছিলুম না তাই হওয়া’। ফলে আমাদের সামাজিক বুদ্ধির মুখে প্রাচীন ভারতবর্ষের দিকে আর আমাদের রাষ্ট্রীয় বুদ্ধির মুখ নবীন ইউরোপের দিকে। এই আদর্শের উভয়সংকটে পড়ে আমরা শিক্ষার একটা সপথ ধরতে পারছি নে— স্কুলেও নয়, সাহিত্যেও নয়।
একজন ইংরেজ দার্শনিক বলেছেন যে, সমস্যাটা যে কি এবং কোথায়, সেইটে ধরাই কঠিন; তার মীমাংসা করা সহজ। একথা সত্য। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ তাই ‘ঘরেবাইরে’য় আমাদের জাতীয় সমস্যার ছবি এঁকেছেন; কেননা, ও-উপন্যাসখানি একটি রূপক-কাব্য ছাড়া আর-কিছুই নয়। নিখিলেশ হচ্ছেন প্রাচীন ভারতবর্ষ, সন্দীপ নবীন ইউরোপ, আর বিমলা বর্তমান ভারত। এই দোটানার ভিতর পড়েই বিমলা বেচারা নাস্তানাবুদ হচ্ছে, মুক্তির পথ যে কোন দিকে, তা সে খুঁজে পাচ্ছে না। এরূপ অবস্থায় এক সৎশিক্ষা ব্যতীত তার উদ্ধারের উপায়ান্তর নেই। অতএব এক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে শিক্ষার একটি আদর্শ খুঁজে-পেতে বার করা দরকার।
আমি বহু গবেষণার ফলেও সে আদর্শ আজও আবিষ্কার করতে পারি নি, সুতরাং সে আদর্শ নিজেই গড়তে বাধ্য হয়েছি। আমি স্বজাতিকে অনুরোধ করি যে, আমার এই গড়া আদর্শ যেন বিনা পরীক্ষায় পরিহার না করেন।
শ্ৰীমতী লীলা মিত্র নামক জনৈক ভদ্রমহিলা ‘সবুজপত্রে’ এই মত প্রকাশ করেন যে, এদেশে শিক্ষার আদর্শ ভুল, সুতরাং তার পদ্ধতিও নিরর্থক। তাঁর মতে আমরা প্রীজাতিকে সেই শিক্ষা দিতে চাই, যাতে তারা পুরুষজাতির কাজে লাগে, সুতরাং সে শিক্ষা নিল। একথা সম্ভবত সত্য। তিনি চান যে শ্রীজাতি নিজের শিক্ষার ভার নিজ-হস্তে গ্রহণ করেন। এ হলে তো আমরা বাঁচি। আমাদের মেয়েরা যদি নিজের বিবাহের ভার নিজের হাতে নেন, তাহলে দেশসুদ্ধ লোক যেমন কন্যাদায় হতে অমনি নিষ্কৃতি লাভ করে, তেমনি মা-লক্ষীরা যদি নিজ-গুণে মা-সরস্বতী হয়ে ওঠেন, তাহলে স্ত্রীশিক্ষার সমস্যা আমাদের আর মীমাংসা করতে হয় না।
সে যাই হোক, আমি বলি, পুরুষজাতিকে সেই শিক্ষা দেওয়া হোক, যাতে তারা স্ত্রীজাতির কাজে লাগে। শিক্ষার এ আদর্শ কোনো কালে কোনো দেশে ছিল না বলেই আমাদের পক্ষে তা গ্রাহ্য করা উচিত। পুরুষজাতি যদি এই আদর্শে শিক্ষিত হয়, তাহলে আর কিছু না হোক, পৃথিবীর মারামারিকাটাকাটি সব থেমে যাবে। নিখিলেশ ও সন্দীপ যদি বিমলাকে নিজের নিজের কাজে লাগাতে চেষ্টা না করে নিজেদের বিমলার কাজে লাগাতে চেষ্টা করতেন, তাহলে গোল তো সব মিটেই যেত। অতএব আমরা যাতে বিমলার কাজে লাগি, সেইরকম আমাদের শিক্ষা হওয়া কর্তব্য।
মাঘ ১৩২২
শিশু-সাহিত্য
যে-কোনো ভাষাতেই হোক না কেন, সমাস-ব্যবহারের ভিতর যে বিপদ আছে, সেবিষয়ে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটক আমাদের সতর্ক করে দিয়েছেন। আমরা যদি কথার গায়ে কথা জড়িয়ে লিখি, তাহলে পাঠকদের পক্ষে তা ছাড়িয়ে নিয়ে পড়া কঠিন। ত্বষ্টা পত্ৰ বত্রকে আশীর্বাদ করেছিলেন ইন্দ্রশ হও’। কিন্তু সমাসের কৃপায় সে বর যে কি মারাত্মক শাপে পরিণত হয়েছিল, তার আমল বিবরণ শতপথ ব্রহণে’ দেখতে পাবেন। সুতরাং পাঠক যাতে উলটো না বোঝেন, সে কারণ এ প্রবন্ধের সমস্ত-নামটির অর্থ প্রথমেই বলে রাখা আবশ্যক। এ প্রবন্ধে ব্যবহৃত শিশু-সাহিত্যের অর্থ বঙ্গসাহিত্য নয়। শিশুদের জন্য বাংলাভাষায় যে সাহিত্যের আজকাল নিত্যনব সৃষ্টি করা হচ্ছে, সেই সাহিত্যই আমার বিচার্য।
শিশু-সাহিত্য বলে কোনো জিনিস আছে কি না, যা বিশেষ করে শিশুদের জন্যই লেখা হয় তাকে সাহিত্য বলা চলে কি না, এবিষয়ে অনেকের মনে বিশেষ সন্দেহ আছে; আমার মনে কিন্তু নেই। আমার দঢ় বিশ্বাস যে, শিশু-সাহিত্য বলে কোনো পদার্থের অস্তিত্ব নেই এবং থাকতে পারে না। কেননা, শিশ-পছন্দ সাহিত্য শিশ, ব্যতীত অপর-কেউ রচনা করতে পারে না, আর শিশুরা সমাজের উপর আর-যে অত্যাচারই করুক-না কেন, সাহিত্যরচনা করে না।
বিলেতে চিলড্রেনের সাহিত্য থাকতে পারে, এদেশে নেই; কেননা, সেদেশের চাইল্ডের সঙ্গে এদেশের শিশুর ঢের তফাত বয়েসে। এদেশে আরকিছু বাড়ুক আর না-বাড়ক, বয়েস বাড়ে; আর সে এত তেড়ে যে, আমাদের ছেলেমেয়েরা যত সত্বর শৈশব অতিক্রম করে, পৃথিবীর অপর কোনো দেশে তত শীঘ্র করে না। অন্তত এই হচ্ছে আমাদের ধারণা। ফলে, যে বয়েসে ইউরোপের মেয়েরা ছেলেখেলা করে, সেই বয়েসে আমাদের মেয়েরা ছেলে মানুষ করে। এবং সেই ছেলে যাতে শীঘ্র মানুষ হয়, সেই উদ্দেশ্যে আমরা শৈশবের মেয়াদ পাঁচ বৎসরের বেশি দিই নে। আজকাল আবার দেখতে পাই, অনেকে তার মধ্যেও দু বছর কেটে নেবার পক্ষপাতী। শৈশবটা হচ্ছে মানবজীবনের পতিত জমি; এবং আমাদের বিশ্বাস, সেই পতিত জমি যত শীঘ্র আবাদ করা যাবে, তাতে তত বেশি সোনা ফলবে।
বাপ-মা’র এই সুবর্ণের লোভবশত এদেশের ছেলেদের বর্ণপরিচয়টা অতি শৈশবেই হয়ে থাকে। একালের শিক্ষিত লোকেরা ছেলে হাঁটতে শিখলেই তাকে পড়তে বসান। শিশুদের উপর এরূপ অত্যাচার করাটা যে ভবিষ্যৎ বাঙালিজাতির পক্ষে কল্যাণকর নয়, সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই; কেননা, যে শৈশবে শিশু ছিল না, সে যৌবনে যুবক হতে পারবে না। আর একথা বলা বাহুল্য, শিশুশিক্ষার উদ্দেশ্যই হচ্ছে শিশুর শিশুত্ব নষ্ট করা; অর্থাৎ যার আনন্দ উপভোগ করবার শক্তি অপরিমিত, তাকে জ্ঞানের ভোগ ভোগানো। সে ভোগ যে কি কর্মভোগ, তা চেষ্টা করলে আমরাও কল্পনা করতে পারি। ধরুন, যদি আমরা স্বর্গে যাবামাত্র স্বগীয় মাস্টারমহাশয়দের দল এসে আমাদের স্বর্গরাজ্যের হিস্টরি-জিওগ্রাফি শেখাতে এবং দেবভাষার শিশবোধ-ব্যাকরণ মুখস্থ করাতে বসান, তাহলে আমাদের মধ্যে ক’জন নির্বাণ-মুক্তির জন্য লালায়িত না হবেন? আর একথাও সত্য যে, শিশর কাছে এ পৃথিবী স্বর্গ। তার কাছে সবই আশ্চর্য, সবই চমৎকার, সবই আনন্দময়।
এসব কথা অবশ্য বলা ব্যথা; কেননা, আমরা শিশুকে শিক্ষা দেবই দেব। মেয়েরা কথায় বলে, ‘পড়লে-শুনলে দুধ-ভাতু, না পড়লে ঠেঙার গুঁতো’; কথাটা অবশ্য ষোলোআনা সত্য নয়। সংসারে প্রায়ই দেখা যায়, সরস্বতীর বরপত্রেরাই লক্ষ্মীর ত্যাজ্যপত্রে। আমাদের কিন্তু মেয়েলি-শাস্ত্রে ভক্তি এত অগাধ যে, আমরা ছেলেদের ভবিষ্যতের দুধে-ভাতুর ব্যবস্থা করবার জন্য বর্তমানে দু, বেলা ঠেঙার গুতোর ব্যবস্থা করি। ছেলেদের দেহমনের উপর মারপিট বছর-সাতেকের জন্য মুলতবি রাখলে যে কিছু ক্ষতি হয়, অবশ্য তা নয়। যে ছেলে সাত বৎসর বয়েসে ‘সিদ্ধির’ লিখবে, তিন-সাত্তা-একুশ বৎসর বয়েসে তার মনস্কামনা নিশ্চয়ই সিদ্ধ হবে; অর্থাৎ সে সাবালক হবার সঙ্গেসঙ্গেই উপাধিগ্রস্ত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় হতে নিষ্কৃতিলাভ করবে। তবে যদি কারও চৌদ্দ বৎসরেও কুলবাস অন্ত না হয়, তাহলে বুঝতে হবে ভগবান তার কপালে উপবাস লিখেছেন। তাকে যতদিন ধরে যতই লেখাও, সে ঐ এক কপালের লেখাই লিখবে।
শিশুশিক্ষা-জিনিসটে আমরা কেউ বন্ধ করতে পারব না, কিন্তু তাই বলে কি আমাদের ও-ব্যাপারের যোগাড় দেওয়া উচিত। সাহিত্যের কাজ তো আর সমাজকে এলেম দেওয়া নয়, আক্কেল দেওয়া। সুতরাং আমরা যদি পাঁচ বছর বয়েসের ছেলের যোগ্য এবং উপভোগ্য সাহিত্য লিখতেও পারি, তাহলেও আশা করি কোনো পাঁচবছরের ছেলে তা পড়তে পারবে না। আর ও-বয়েসের কোনো ছেলে যদি পঠন-পাঠনে অভ্যস্ত হয়, তাহলে তার হাতে শিশু-সাহিত্য নয়, বেদান্ত দেওয়া কর্তব্য। কেননা, সে যত শীঘ্র ‘বালাযযাগী’ হয়, তত তার এবং সমাজের উভয়েরই পক্ষে মঙ্গল। প্রথমত, ওরকম ছেলের বাঁচা কঠিন, আর যদি সে বাঁচে তাহলে সমাজের বাঁচা কঠিন; কেননা, অমন সুপুত্র বাঁচলে— হয় একটি বিগ্রহ, নয় গ্রহ হতে বাধ্য। অকালপক্কতার প্রশ্রয় দেওয়াটা একেবারেই অন্যায়; কেননা, কাঁচা একদিন পাকতে পারে, কিন্তু অকালপক্ক আর ইইজীবনে কাঁচতে পারে না। ইতিহাসে এর প্রমাণ আছে। শিক্ষাবাতিকগ্রস্ত বাপের তাড়নায় বারো বৎসর বয়েসে সর্বশাস্ত্রে পারগামী হওয়ার দরুন জন, স্টুয়ার্ট মিল,এর হদয়-মন যে কতদূর ইচড়ে পেকে গিয়েছিল, তার পরিচয় তিনি নিজমুখেই দিয়েছেন। ফলে, তিনি বদ্ধবয়সে কাঁচতে গিয়ে বিবাহ করেন।
অতএব দাঁড়াল এই যে, শিশু-সাহিত্য বলে কোনো জিনিস নেই এবং থাকা উচিত নয়। তবে শিশুপাঠ্য না হোক, বালপাঠ্য সাহিত্য আছে এবং থাকা উচিত। এ সাহিত্য সৃষ্টি করবার সংকল্প অতি সাধ। কেননা, শিশুশিক্ষার পুস্তকে যে বস্তু বাদ পড়ে যায় অর্থাৎ আনন্দ–সেই বস্তু যুগিয়ে দেবার উদ্দেশ্যেই এ সাহিত্যের সৃষ্টি। পৃথিবীতে অবশ্য সাধসংকল্পমাত্রেই আমরা কার্যে পরিণত করতে পারি নে। সুতরাং এখলে জিজ্ঞাস্য— আমরা পণ করে বসলেই কি সে সাহিত্য রচনা করতে পারব? আমি বলি, না। এর প্রমাণ, ছেলেরা যে সাহিত্য পড়ে আর পড়তে ভালোবাসে, তা মুখ্যত কি গৌণত ছেলেদের জন্য নয়, বড়দের জন্যই লেখা হয়েছিল। রূপকথা রামায়ণ মহাভারত আরব্য-উপন্যাস ডন-কুইকসোট গালিভার’স-ট্র্যাভেলস, রবিনসন-সো— এসবের কোনোটিই আদিতে শিশুদের জন্য রচিত হয় নি। এর থেকেই প্রমাণ হয় যে, উচ্চ-অগের সাহিত্যেরই একটি বিশেষ অঙ্গ ছেলেরা আত্মসাৎ করে নেয়।
আসলে, ছেলেরা ভালোবাসে শুধু রূপকথা–স্বরূপ কথাও নয়, অরূপ কথাও নয়; অর্থাৎ জ্ঞানের কথাও নয়, নীতির কথাও নয়। উপরে যেসব বইয়ের নাম করা গেল, তার প্রতিটিতেই রূপকথার রূপ আছে। আমরা যে শিশসাহিত্য রচনা করতে পারি নে, তার কারণ আমরা চেষ্টা করলেও রূপকথা তৈরি করতে পারি নে। যে যুগে রূপেকথার সৃষ্টি হয়, সে যুগ হচ্ছে মানবসভ্যতার শৈশব। সেকালে লোক মনে শিশ ছিল, সে যুগে সম্ভব-অসম্ভবের ভেদজ্ঞান মানুষের মনে তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। একালের আমরা মনে জানি সবই অসম্ভব, আর ছেলেরা মনে করে সবই সম্ভব। তাছাড়া, আমাদের কাছে পৃথিবীর সব জিনিসই আবশ্যক, কোনো জিনিসই চমৎকার নয়; আর ছেলেদের কাছে সব জিনিসই চমৎকার, কোনো জিনিসই আবশ্যক নয়। সুতরাং আমাদের পক্ষে তাদের মনোমত সাহিত্য রচনা করা অসম্ভব। আমরা রূপকথা লিখতে বসলে, হয় তা কিছুই হবে না, নয় রূপক হবে; কেননা, রূপকথার জন্ম সত্যযুগে, আর রূপকের জন্ম সভ্যযুগে।
এই রূপকের মধ্যেই হাজারে একখানা ছেলেদের কাছে নবরুপকথা হয়ে দাঁড়ায়, যথা ডন-কুইকসোট গালিভার’স-ট্রাভেলস ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, এ জাতের রূপকথা রচনা করবার জন্য অসামান্য প্রতিভার আবশ্যক। অসম্ভবকে সম্ভব, কল্পনাকে বাস্তব করে তোলা এককথায়, বস্তুজগতের নিয়ম অতিক্রম করে একটি নববস্তুজগৎ গড়ে তোলা তোমার-আমার কর্ম নয়। আর যাঁর অসামান্য প্রতিভা আছে, তাঁর বই-লেখার উদ্দেশ্য ছেলেদের এ বোঝানো নয় যে, তারা মনে পাকা; কিন্তু বুড়োদের এই বোঝানো যে, তারা মনে কাঁচা। বয়েসে বদ্ধ কিন্তু মনে বালক–এমন সাহিত্যিক যে নেই, একথা আমি বলতে চাই নে। কিন্তু সে সাহিত্যিকের দ্বারাও শিশু-সাহিত্য রচিত হতে পারে না, তার কারণ ছোটছেলে ও বড়োখোকা— এ দুই একজাতীয় জীব নয়। বয়স্কলোকের বালিশতার মূল হচ্ছে সত্য ধরবার অক্ষমতা, আর বালকের বালকত্বের মূল হচ্ছে কল্পনা করবার সক্ষমতা। সুতরাং আমার মতে, বিশেষ করে শিশু-সাহিত্য রচনা হতে আমাদের নিরস্ত থাকাই শ্রেয়। আমরা যদি ঠিক আমাদের-উপযোগী বই লিখি, খুব সম্ভবত তা শিশু-সাহিত্যই হবে।
অগ্রহায়ণ ১৩২৩
সবুজপত্র
বাংলাদেশ যে সবুজ, একথা বোধ হয় বাহ্যজ্ঞানশূন্য লোকেও অস্বীকার করবেন না। মা’র শস্যশ্যামলরপ বাংলার এত গদ্যেপদ্যে এতটা পল্লবিত হয়ে উঠেছে যে, সে বর্ণনার যাথার্থ বিবাস করবার জন্য চোখে দেখবারও আবশ্যক। নেই। পনেরক্তির গুণে এটি সেই শ্রেণীর সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার সম্বন্ধে চক্ষুকণের যে বিবাদ হতে পারে, এরূপ সন্দেহ আমাদের মনে মহতের জন্যও স্থান পায় না। এক্ষেত্রে সৌভাগ্যবশত নাম ও রূপের বাস্তবিকই কোনো বিরোধ নেই। একবার চোখ তাকিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, তরাই হতে সুন্দরবন পর্যন্ত এক ঢালা সবুজবৰ্ণ দেশটিকে আদ্যোপান্ত ছেয়ে রেখেছে। কোথাও তার বিচ্ছেদ নেই, কোথাও তার বিরাম নেই। শুধু তাই নয়, সেই রং বাংলার সীমানা অতিক্রম করে উত্তরে হিমালয়ের উপরে ছাপিয়ে উঠেছে ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের ভিতর চারিয়ে গেছে।
সবুজ, বাংলার শুধু, দেশজোড়া রং নয়–বারোমেসে রং। আমাদের দেশে প্রকৃতি বহুরূপী নয়, এবং ঋতুর সঙ্গেসঙ্গে বেশ পরিবর্তন করে না। বসন্তে বিয়ের কনের মত ফলের জহরতে আপাদমস্তক সালংকারা হয়ে দেখা দেয় না, বর্ষার জলে শুচিস্নাতা হয়ে শরতের পূজার তসর ধারণ করে আসে না, শীতে বিধবার মত শাদা শাড়িও পরে না। মাধব হতে মধ পর্যন্ত ঐ সবুজের টানা সুর চলে; ঋতুর প্রভাবে সে সুরের যে রূপান্তর হয়, সে শুধু কড়িকোমলে। আমাদের দেশে অবশ্য বর্ণের বৈচিত্র্যের অভাব নেই। আকাশে ও জলে, ফলে ও ফলে আমরা বর্ণগ্রামের সকল সুরেরই খেলা দেখতে পাই। কিন্তু মেঘের রং ও ফলের রং ক্ষণস্থায়ী; প্রকৃতির ওসকল রাগরঙ্গ তার বিভাব ও অভাব মাত্র। তার স্থায়ী ভাবের, তার মূল রসের পরিচয় শুধু সবজে। পাঁচরঙা ব্যাভিচারীভাবসকলের সার্থকতা হচ্ছে বঙ্গদেশের এই অখণ্ডহরিৎ স্থায়ী ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলা।
এরূপ হবার অবশ্য একটা অর্থ আছে। বর্ণমাত্রেই ব্যঞ্জন বর্ণ; অর্থাৎ বর্ণের উদ্দেশ্য শুধু বাহ্যবস্তুকে লক্ষণান্বিত করা নয়, কিন্তু সেই সুযোগে নিজেকেও ব্যক্ত করা। যা প্রকাশ নয়, তা অপর কিছুই প্রকাশ করতে পারে না। তাই রং রূপও বটে, রূপকও বটে। যতক্ষণ আমাদের বিভিন্ন বর্ণের বিশেষ ব্যক্তিত্বের জ্ঞান না জন্মায়, ততক্ষণ আমাদের প্রকৃতির বর্ণপরিচয় হয় না এবং আমরা তার বক্তব্য কথা বুঝতে পারি নে। বাংলার সবুজপত্রে যে সুসমাচার লেখা আছে, তা পড়বার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক হবার আবশ্যক নেই। কারণ সে লেখার ভাষা বাংলার প্রাকৃত। তবে আমরা সকলে যে তার অর্থ বুঝতে পারি নে, তার কারণ হচ্ছে যিনি গুপ্ত জিনিস আবিষ্কার করতে ব্যস্ত, ব্যক্ত জিনিস তাঁর চোখে পড়ে না।
যাঁর ইন্দ্রধনুর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় আছে আর তার জন্মকথা জানা আছে, তিনিই জানেন যে, সূর্যকিরণ নানা বর্ণের একটি সমন্টিমাত্র এবং শুধু সিধে পথেই সে শাদা ভাবে চলতে পারে। কিন্তু তার সরল গতিতে বাধা পড়লেই সে সমষ্টি ব্যস্ত হয়ে পড়ে, বক্র হয়ে বিচিত্র ভঙ্গি ধারণ করে, এবং তার বর্ণসকল পাঁচ বর্গে বিভক্ত হয়ে যায়। সবুজ হচ্ছে এই বর্ণমালার মধ্যমণি, এবং নিজগুণেই সে বর্ণরাজ্যের কেন্দ্রস্থল অধিকার করে থাকে; বেগুনি কিশলয়ের রং, জীবনের পরাগের রং; লাল রক্তের রং, জীবনের পর্ণেরাগের রং; নীল আকাশের রং, অনন্তের রং; পীত শপত্রের রং, মৃত্যুর রং। কিন্তু সবুজ হচ্ছে নবীন পত্রের রং, রসের ও প্রাণের যুগপৎ লক্ষণ ও ব্যক্তি; তার দক্ষিণে নীল আর বামে পীত, তার পবসীমায় বেগুনি আর পশ্চিমসীমায় লাল। অত ও অনন্তের মধ্যে, পূর্বে ও পশ্চিমের মধ্যে, স্মৃতি ও আশার মধ্যে মধ্যস্থতা করাই হচ্ছে সবরে, অর্থাৎ সরস প্রাণের, স্বধর্ম।
যে বর্ণ বাংলার ওষধিতে ও বনতিতে নিত্য বিকশিত হয়ে উঠছে, নিশ্চয় সেই একই বর্ণ আমাদের হদয়-মনকেও রঙিয়ে রেখেছে। আমাদের বাহিরের প্রকৃতির যে রং, আমাদের অন্তরের পুরুষেরও সেই রং। একথা যদি সত্য হয়, তাহলে সজীবতা ও সরসতই হচ্ছে বাঙালির মনের নৈসর্গিক ধর্ম। প্রমাণস্বরূপে দেখানো যেতে পারে যে, আমাদেব দেবতা হয় শ্যাম নয় শ্যামা। আমাদের হদয়মন্দিরে রজতগিরিসভি কিংTI জবাকুসুমসংকাশ দেবতার স্থান নেই; আমরা শৈবও নই, সৌরও নই।
আমরা হয় বৈষ্ণব, নয় শাক্ত। এ উভয়ের মধ্যে বাঁশি ও অসির যা প্রভেদ, সেই পার্থক্য বিদ্যমান; তবও বর্ণসামান্যতার গুণে শ্যাম ও শ্যামা আমাদের মনের ঘরে নির্বিবাদে পাশাপাশি অবস্থিতি করে। তবে বঙ্গসরস্বতীর দবাদলশ্যামরপ আমাদের চোখে যে পড়ে না, তার জন্য দোষী আমরা নই, দোষী আমাদের শিক্ষা। একালের বাণীর মন্দির হচ্ছে বিদ্যালয়। সেখানে আমাদের গররা এবং গরজনেরা যে জড় ও কঠিন শ্বেতাঙ্গী ও শ্বেতবসনা পাষাণমতির প্রতিষ্ঠা করেছেন, আমাদের মন তার কায়িক এবং বাচিক সেবায় দিন-দিন নীরস ও নিজীব হয়ে পড়ছে। আমরা যে নিজের আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করি নে, তার কারণ আমাদের নিজের সঙ্গে আমাদের কেউ পরিচয় করিয়ে দেয় না। আমাদের সমাজ ও শিক্ষা দুই আমাদের ব্যক্তিত্বের বিরোধী। সমাজ শাধ একজনকে আর-পাঁচজনের মত হতে বলে, ভুলেও কখনো আর-পাঁচজনকে একজনের মত হতে বলে না। সমাজের ধর্ম হচ্ছে প্রত্যেকের স্বধর্ম নষ্ট করা। সমাজের যা মন্ত্র, তারই সাধনপদ্ধতির নাম শিক্ষা। তাই শিক্ষার বিধি হচ্ছে ‘অপরের মত হও’, আর তার নিষেধ হচ্ছে নিজের মত হয়ো না। এই শিক্ষার কৃপায় আমাদের মনে এই অদ্ভুত সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, আমাদের স্বধর্ম এতই ভয়াবহ যে তার চাইতে পরধর্মে নিধনও শ্রেয়। সুতরাং কাজে ও কথায়, লেখায় ও পড়ায়, আমরা আমাদের মনের সরস সতেজ ভাবটি নষ্ট করতে সদাই উৎসুক। এর কারণও স্পষ্ট, সবুজ রং ভালোমন্দ দুই অর্থেই কাঁচা। তাই আমাদের কর্মযোগীরা আর জ্ঞানযোগীরা, অর্থাৎ শাস্ত্রীর দল, আমাদের মনটিকে রাতারাতি পাকা করে তুলতে চান। তাঁদের বিশ্বাস যে, কোনোরূপ কর্ম কিংবা জ্ঞানের চাপে আমাদের হৃদয়ের রসটুকু নিংড়ে ফেলতে পারলেই আমাদের মনের রং পেকে উঠবে। তাঁদের রাগ এই যে, সবুজ বর্ণমালার অন্তস্থ বর্ণ নয়, এবং ও রং কিছুরই অতে আসে না জীবনেরও নয়, বেদেরও নয়, কমেরও নয়, জ্ঞানেরও নয়। এদের চোখে সবুজ মনের প্রধান দোষ যে, সে মন পর্বমীমাংসার অধিকার ছাড়িয়ে এসেছে এবং উত্তরমীমাংসার দেশে গিয়ে পৌঁছয় নি। এরা ভুলে যান যে, জোর করে পাকাতে গিয়ে আমরা শুধু হরিৎকে পীতের ঘরে টেনে আনি, প্রাণকে মৃত্যুর দ্বারস্থ করি। অপরদিকে এদেশের ভক্তিযোগীরা, অর্থাৎ কবির দল, কাঁচাকে কচি করতে চান। এরা চান যে, আমরা শুধু গদগদভাবে আধ-আধ কথা কই। এদের রাগ সবুজের সজীবতার উপর। এদের ইচ্ছা, সবুজের তেজক বহিস্কৃত করে দিয়ে ছাঁকা রসটকু রাখেন। এরা ভুলে যান যে, পাতা কখনো আর কিশলয়ে ফিরে যেতে পারে না। প্রাণ পশ্চাৎপদ হতে জানে না; তার ধর্ম হচ্ছে এগনো, তার লক্ষ্য হচ্ছে হয় অমতত্ব নয় মৃত্যু। যে মন একবার কমের তেজ ও জ্ঞানের ব্যোমের পরিচয় লাভ করেছে, সে এ উভয়কে অন্তরঙ্গ করবেই কেবলমাত্র ভক্তির শান্তিজলে সে তার সমস্ত হদয় পূর্ণ করে রাখতে পারে না। আসল কথা হচ্ছে, তারিখ এগিয়ে কিংবা পিছিয়ে দিয়ে যৌবনকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। এ উভয়ের সমবেত চেষ্টার ফল দাঁড়িয়েছে এই যে, বাঙালির মন এখন অর্ধেক অকালপক্ক, এবং অর্ধেক অযথা-কচি। আমাদের আশা আছে যে, সবুজ ক্ৰমে পেকে লাল হয়ে উঠবে। কিন্তু আমাদের অন্তরের আজকের সবুজরস কালকের লালরক্তে তবেই পরিণত হবে, যদি আমরা স্বধর্মের পরিচয় পাই, এবং প্রাণপণে তার চর্চা করি। আমরা তাই দেশী কি বিলেতি পাথরে-গড়া সরস্বতীর মতির পরিবর্তে বাংলার কাব্যমন্দিরে দেশের মাটির ঘট স্থাপনা করে তার মধ্যে সবজেপত্রের প্রতিষ্ঠা করতে চাই। কিন্তু এ মন্দিরের কোনো গভমন্দির থাকবে না, কারণ সবুজের পর্ণ অভিব্যক্তির জন্য আলো চাই আর বাতাস চাই। অন্ধকারে সবুজ ভয়ে নীল হয়ে যায়; বন্ধ ঘরে সবুজ দঃখে পাণ্ডু হয়ে যায়। আমাদের নব-মন্দিরের চারিদিকের অবারিত দ্বার দিয়ে প্রাণবায়ুর সঙ্গেসঙ্গে বিশ্বের যত আলো অবাধে প্রবেশ করতে পারবে। শুধু তাই নয়, এ মন্দিরে সকল বর্ণের প্রবেশের সমান অধিকার থাকবে। উষার গোলাপি, আকাশের নীল, সন্ধ্যার লাল, মেঘের নীললোহিত, বিরোধালংকারস্বরূপে সবুজপত্রের গাত্রে সংলগ্ন হয়ে তার মরকতদ্যতি কখনো উজ্জ্বল কখনো কোমল করে তুলবে। সে মন্দিরে স্থান হবে না কেবল শুষ্কপত্রের।
বৈশাখ ১৩২১
সাহিত্যে খেলা
জগৎবিখ্যাত ফরাসি ভাস্কর রোড্যাঁ, যিনি নিতান্ত জড় প্রস্তরের দেহ থেকে অসংখ্য জীবিতপ্রায় দেবদানব কেটে বার করেছেন, তিনিও, শুনতে পাই, যখন-তখন হাতে কাদা নিয়ে আঙুলের টিপে মাটির পুতুল তয়ের করে থাকেন। এই পুতুল-গড়া হচ্ছে তাঁর খেলা। শুধু রোড্যাঁ কেন, পৃথিবীর শিল্পীমাত্রেই এই শিল্পের খেলা খেলে থাকেন। যিনি গড়তে জানেন, তিনি শিবও গড়তে পারেন, বাঁদরও গড়তে পারেন। আমাদের সঙ্গে বড়-বড় শিল্পীদের তফাত এইটুকু যে, তাঁদের হাতে এক করতে আর হয় না। সম্ভবত এই কারণে কলারাজ্যের মহাপুরুষদের যা-খুশি-তাই করবার যে অধিকার আছে, ইতর শিল্পীদের সে অধিকার নেই। স্বর্গ হতে দেবতারা মধ্যেমধ্যে ভূতলে অবতীর্ণ হওয়াতে কেউ আপত্তি করেন না, কিন্তু মর্তবাসীদের পক্ষে রসাতলে গমন করাটা বিশেষ নিন্দনীয়। অথচ একথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, যখন এ জগতে দশটা দিক আছে, তখন এইসব-দিকেই গতায়াত করবার প্রবত্তিটি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। মন উচুতেও উঠতে চায়, নীচুতেও নামতে চায়; বরং সত্যকথা বলতে গেলে, সাধারণ লোকের মন স্বভাবতই যেখানে আছে তারই চারপাশে ঘুরে বেড়াতে চায় উড়তেও চায় না, ডুবতেও চায় না। কিন্তু সাধারণ লোকে সাধারণ লোককে, কি ধর্ম, কি নীতি, কি কাব্য সকল রাজ্যেই অহরহ ডানায় ভর দিয়ে থাকতেই পরামর্শ দেয়। একটু উচুতে না চড়লে আমরা দর্শক এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর নয়ন-মন আকর্ষণ করতে পারি নে। বেদিতে না বসলে আমাদের উপদেশ কেউ মানে না, রঙ্গমঞ্চে না চড়লে আমাদের অভিনয় কেউ দেখে না, আর কাঠমঞ্চে না দাঁড়ালে আমাদের বক্তৃতা কেউ শোনে না। সুতরাং জনসাধারণের চোখের সম্মখে থাকবার লোভে আমরাও অগত্যা চব্বিশঘণ্টা টঙে চড়ে থাকতে চাই, কিন্তু পারি নে। অনেকের পক্ষে নিজের আয়ত্তের বহির্ভূত উচ্চস্থানে ওঠবার চেষ্টাটাই মহাপতনের কারণ হয়। এসব কথা বলবার অর্থ এই যে, কষ্টকর হলেও আমাদের পক্ষে অবশ্য মহাজনদের পথ অনুসরণ করাই কর্তব্য; কিন্তু ডাইনে বাঁয়ে ছোটখাট গলিঘজিতে খেলাচ্ছলে প্রবেশ করবার যে অধিকার তাঁদের আছে, সে অধিকারে আমরা কেন বঞ্চিত হব। গান করতে গেলেই যে সুর তারায় চড়িয়ে রাখতে হবে, কবিতা লিখতে হলেই যে মনের শুধু গভীর ও প্রখর ভাব প্রকাশ করতে হবে, এমন-কোনো নিয়ম থাকা উচিত নয়। শিল্পরাজ্যে খেলা করবার প্রবৃত্তির ন্যায় অধিকারও বড়-ছোট সকলেরই সমান আছে। এমনকি, একথা বললেও অত্যুক্তি হয় না যে, এ পৃথিবীতে একমাত্র খেলার ময়দানে ব্রাহ্মণ-শদ্রের প্রভেদ নাই। রাজার ছেলের সঙ্গে দরিদ্রের ছেলেরও খেলায় যোগ দেবার অধিকার আছে। আমরা যদি একবার সাহস করে কেবলমাত্র খেলা করবার জন্য সাহিত্যজগতে প্রবেশ করি, তাহলে নির্বিবাদে সে জগতের রাজারাজড়ার দলে মিশে যাব। কোনোরূপ উচ্চ আশা নিয়ে সেক্ষেত্রে উপস্থিত হলেই নিম্ন শ্রেণীতে পড়ে যেতে হবে।
২.
লেখকেরাও অবশ্য দলের কাছে হাততালির প্রত্যাশা রাখেন, বাহবা না পেলে মনঃক্ষুণ্ণ হন; কেননা, তাঁরাই হচ্ছেন যথার্থ সামাজিক জীব, বাদবাকি সকলে কেবলমাত্র পারিবারিক। বিশ্বমানবের মনের সঙ্গে নিত্যনূতন সম্বন্ধ পাতানোই হচ্ছে কবি-মনের নিত্যনৈমিত্তিক কম। এমনকি, কবির আপন মনের গোপন কথাটিও গীতিকবিতাতে রঙ্গভূমির স্বগতোক্তিস্বরূপেই উচ্চারিত হয়, যাতে করে সেই মর্মকথা হাজার লোকের কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু উচ্চমঞ্চে আরোহণ করে উচ্চৈঃস্বরে উচ্চবাচ্য করলে যে জনসাধারণের নয়নমন আকর্ষণ করা যায় না, এমন-কোনো কথা নেই। সাহিত্যজগতে যাঁদের খেলা করবার প্রবত্তি আছে, সাহস আছে ও ক্ষমতা আছে— মানুষের নয়ন-মন আকর্ষণ করবার সুযোগ বিশেষ করে তাঁদের কপালেই ঘটে। মানুষে যে খেলা দেখতে ভালোবাসে, তার পরিচয় তো আমরা এই জড় সমাজেও নিত্যই পাই। টাউনহলে বক্তৃতা শুনতেই বা ক’জন যায় আর গড়ের মাঠে ফটবল-খেলা দেখতেই বা ক’জন যায়। অথচ একথাও সত্য যে, টাউন-হলের বক্তৃতার উদ্দেশ্য অতি মহৎ— ভারত-উদ্ধার; আর গড়ের মাঠের খেলোয়াড়দের ছটোছটি দৌড়াদৌড়ি আগাগোড়া অর্থশন্য এবং উদ্দেশ্যবিহীন। আসল কথা এই যে, মানুষের দেহমনের সকলপ্রকার ক্রিয়ার মধ্যে ক্রীড়া শ্রেষ্ঠ; কেননা, তা উদ্দেশ্যহীন। মানুষে যখন খেলা করে, তখন সে এক আনন্দ ব্যতীত অপরকোনো ফলের আকাক্ষা রাখে না। যে খেলার ভিতর আনন্দ নেই কিন্তু উপরি-পাওনার আশা আছে, তার নাম খেলা নয়, জয়াখেলা। ও-ব্যাপার সাহিত্যে চলে না; কেননা, ধমত জয়াখেলা লক্ষ্মীপজার অগ, সরস্বতীপূজার নয়। এবং যেহেতু খেলার আনন্দ নিরর্থক অর্থাৎ অর্থগত নয়, সে কারণ তা কারও নিজস্ব হতে পারে না। এ আনন্দে সকলেরই অধিকার সমান।
সুতরাং সাহিত্যে খেলা করবার অধিকার যে আমাদের আছে, শুধু তাই নয়— স্বার্থ এবং পরাধএ দুয়ের যুগপৎ সাধনের জন্য মনোজগতে খেলা করাই হচ্ছে আমাদের পক্ষে সর্বপ্রধান কর্তব্য। যে লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে ফলের চাষ করতে ব্রতী হন, যিনি কোনোরূপ কার্য-উদ্ধারের অভিপ্রায়ে লেখনী ধারণ করেন, তিনি গীতের মর্মও বোঝেন না, গীতার ধর্মও বোঝেন না; কেননা, খেলা হচ্ছে জীবজগতে একমাত্র নিষ্কাম কর্ম, অতএব মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। স্বয়ং ভগবান বলেছেন, যদিচ তাঁর কোনোই অভাব নেই তবুও তিনি এই বিশ্ব সজন করেছেন, অর্থাৎ সৃষ্টি তাঁর লীলামাত্র। কবির সৃষ্টিও এই বিশ্বসৃষ্টির অনুরুপ, সে সজনের মূলে কোনো অভাব দূর করবার অভিপ্রায় নেই সে সৃষ্টির মূল অন্তরাত্মার ক্ষতি এবং তার ফল আনন্দ। এককথায় সাহিত্যসৃষ্টি জীবাত্মার লীলামাত্র, এবং সে লীলা বিলীলার অন্তর্ভূত; কেননা, জীবাত্মা পরমাত্মার অঙ্গ এবং অংশ।
৩.
সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া, কারও মনোরঞ্জন করা নয়। এ দুয়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে পরের জন্যে খেলনা তৈরি করতে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন করতে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্মচ্যুত হয়ে পড়ে, তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ নয়। কাব্যের ঝমঝমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙালাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্মের জয়ঢাক— এইসব জিনিসে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে। সাহিত্যরাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের মনস্তুষ্টি হতে পারে কিন্তু তা গড়ে লেখকের মনস্তুষ্টি হতে পারে না। কারণ পাঠকসমাজ যে খেলনা আজ আদর করে, কাল সেটিকে ভেঙে ফেলে; সে প্রাচ্যই হোক আর পাশ্চাত্যই হোক, কাশীরই হোক আর জমানিরই হোক, দু দিন ধরে তা কারও মনোরঞ্জন করতে পারে না। আমি জানি যে, পাঠকসমাজকে আনন্দ দিতে গেলে তাঁরা প্রায়শই বেদনা বোধ করে থাকেন। কিন্তু এতে ভয় পাবার কিছুই নেই; কেননা, কাব্যজগতে যার নাম আনন্দ, তারই নাম বেদনা। সে যাই হোক, পরের মনোরঞ্জন করতে গেলে সরস্বতীর বরপুত্রও যে নটবিটের দলভুক্ত হয়ে পড়েন, তার জাজল্যমান প্রমাণ স্বয়ং ভারতচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জন করতে বাধ্য না হলে তিনি বিদ্যাসন্দর রচনা করতেন না, কিন্তু তাঁর হাতে বিদ্যা ও সুন্দরে অপূর্ব মিলন সংঘটিত হত; কেননা, knowledge এবং art উভয়ই তাঁর সম্পর্ক করায়ত্ত ছিল। ‘বিদ্যাসুন্দর’ খেলনা হলেও রাজার বিলাসভবনের পাঞ্চালিকা— সবর্ণে গঠিত, সুগঠিত এবং মণিমুক্তায় অলংকৃত; তাই আজও তার যথেষ্ট মূল্য আছে, অন্তত জহরির কাছে। অপরপক্ষে, এ যুগে পাঠক হচ্ছে জনসাধারণ; সুতরাং তাঁদের মনোরঞ্জন করতে হলে আমাদের অতি শস্তা খেলনা গড়তে হবে, নইলে তা বাজারে কাটবে না। এবং শস্তা করার অর্থ খেলো করা। বৈশ্য লেখকের পক্ষেই শদ পাঠকের মনোরঞ্জন করা সংগত। অতএব সাহিত্যে আর যাই কর না কেন, পাঠকসমাজের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা কোরো না।
৪.
তবে কি সাহিত্যের উদ্দেশ্য লোককে শিক্ষা দেওয়া?–অবশ্য নয়। কেননা, কবির মতিগতি শিক্ষকের মতিগতির সম্পূর্ণ বিপরীত। স্কুল না বন্ধ হলে যে খেলার সময় আসে না, এ তো সকলেরই জানা কথা। কিন্তু সাহিত্যরচনা যে আত্মার লীলা, একথা শিক্ষকেরা স্বীকার করতে প্রস্তুত নন। সুতরাং শিক্ষা ও সাহিত্যের ধর্মকর্ম যে এক নয়, এ সত্যটি একটু স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়া আবশ্যক। প্রথমত, শিক্ষা হচ্ছে সেই বস্তু, যা লোকে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গলাধঃকরণ করতে বাধ্য হয়, অপরপক্ষে কাব্যরস লোকে শুধু স্বেচ্ছায় নয়, সানন্দে পান করে; কেননা, শাস্ত্রমতে সে রস অমত। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনকে বিশ্বের খবর জানানো; সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের মনকে জাগানো। কাব্য যে সংবাদপত্র নয়, একথা সকলেই জানেন। তৃতীয়ত, অপরের মনের অভাব পর্ণ করবার উদ্দেশ্যেই শিক্ষকের হস্তে শিক্ষা জন্মলাভ করেছে, কিন্তু কবির নিজের মনের পরিপূর্ণতা হতেই সাহিত্যের উৎপত্তি। সাহিত্যের উদ্দেশ্য যে আনন্দদান করা শিক্ষাদান করা নয়–একটি উদাহরণের সাহায্যে তার অকাট্য প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। বাল্মীকি আদিতে মনিঋষিদের জন্য রামায়ণ রচনা করেছিলেন, জনগণের জন্য নয়। একথা বলা বাহুল্য যে, বড়-বড় মনিঋষিদের কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু রামায়ণ শ্রবণ করে মহর্ষিরাও যে কতদূর আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন, তার প্রমাণ— তাঁরা কুশীলবকে তাঁদের যথাসর্বস্ব, এমনকি কৌপীন পর্যন্ত, পেলা দিয়েছিলেন। রামায়ণ কাব্য হিসাবে যে অমর এবং জনসাধারণ আজও যে তার শ্রবণে-পঠনে আনন্দ উপভোগ করে, তার একমাত্র কারণ আনন্দের ধর্মই এই যে তা সংক্রামক। অপরপক্ষে, লাখে একজনও যে যোগ-বাশিষ্ঠ রামায়ণের ছায়া মাড়ান না, তার কারণ সে বহু লোককে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল, আনন্দ দেবার জন্যে নয়। আসল কথা এই যে, সাহিত্য কস্মিনকালেও স্কুলমাস্টারির ভার নেয় নি। এতে দুঃখ করবার কোনো কারণ নেই। দুঃখের বিষয় এই যে, স্কুলমাস্টারেরা একালে সাহিত্যের ভার নিয়েছেন।
কাব্যরসনামক অমতে যে আমাদের অরুচি জন্মেছে, তার জন্য দায়ী এ যুগের স্কুল এবং তার মাস্টার। কাব্য পড়বার ও বোঝবার জিনিস; কিন্তু স্কুলমাস্টারের কাজ হচ্ছে বই পড়ানো ও বোঝানো। লেখক এবং পাঠকের মধ্যে এখন স্কুলমাস্টার দণ্ডায়মান। এই মধ্যস্থদের কৃপায় আমাদের সঙ্গে কবির মনের মিলন দূরে যাক, চারচক্ষুর মিলনও ঘটে না। স্কুলঘরে আমরা কাব্যের রূপে দেখতে পাই নে, শুধু তার গুণ শনি। টীকা-ভাষ্যের প্রসাদে আমরা কাব্য সম্বন্ধে সকল নিগুঢ়তত্ত্ব জানি; কিন্তু সে যে কি বস্তু, তা চিনি নে। আমাদের শিক্ষকদের প্রসাদে আমাদের এ জ্ঞান লাভ হয়েছে যে, পাথরে কয়লা হীরার সবর্ণ না হলেও সগোত্র; অপরপক্ষে, হীরক ও কাঁচ যমজ হলেও সহোদর নয়। এর একের জন্ম পৃথিবীর গর্ভে, অপরটির মানুষের হাতে; এবং এ উভয়ের ভিতর এক দা-কুমড়ার সম্বন্ধ ব্যতীত অপর-কোনো সম্বন্ধ নেই। অথচ এত জ্ঞান সত্ত্বেও আমরা সাহিত্যে কাঁচকে হীরা এবং হীরাকে কাঁচ বলে নিত্য ভুল করি; এবং হীরা ও কয়লাকে একশ্রেণীভুক্ত করতে তিলমাত্র দ্বিধা করি নে; কেননা, ওরূপ করা যে সংগত, তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আমাদের মুখস্থ আছে। সাহিত্য শিক্ষার ভার নেয় না, কেননা মনোজগতে শিক্ষকের কাজ হচ্ছে কবির কাজের ঠিক উলটো। কবির কাজ হচ্ছে কাব্য সৃষ্টি করা, আর শিক্ষকের কাজ হচ্ছে প্রথমে তা বধ করা, তার পরে তার শবচ্ছেদ করা এবং ঐ উপায়ে তার তত্ত্ব আবিষ্কার করা ও প্রচার করা। এইসব কারণে নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, কারও মনোরঞ্জন করাও সাহিত্যের কাজ নয়, কাউকে শিক্ষা দেওয়াও নয়। সাহিত্য ছেলের হাতের খেলনাও নয়, গরুর হাতের বেতও নয়। বিচারের সাহায্যে এই মাত্রই প্রমাণ করা যায়। তবে বস্তু যে কি, তার জ্ঞান অনুভূতিসাপেক্ষ, তর্কসাপেক্ষ নয়। সাহিত্যে মানবাত্মা খেলা করে এবং সেই খেলার আনন্দ উপভোগ করে; এ কথার অর্থ যদি স্পষ্ট না হয়, তাহলে কোনো সুদীর্ঘ ব্যাখ্যার দ্বারা তা স্পষ্টতর করা আমার অসাধ্য।
এইসব কথা শুনে আমার জনৈক শিক্ষাভক্ত বন্ধ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, সাহিত্য খেলাচ্ছলে শিক্ষা দেয়। একথার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, সরস্বতীকে কিন্ডারগার্টেনের শিক্ষয়িত্ৰীতে পরিণত করবার জন্য যতদূর শিক্ষাবাতিকগ্রস্ত হওয়া দরকার, আমি আজও ততদুর হতে পারি নি।
শ্রাবণ ১৩২২
সাহিত্যে চাবুক
সেদিন স্টার-থিয়েটারে ‘আনন্দ-বিদায়ে’র অভিনয় শেষে দক্ষযজ্ঞের অভিনয়ে পরিণত হয়েছিল শুনে দুঃখিত এবং লজ্জিত হলুম। তার প্রথম কারণ এই যে, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মত লোককে দর্শকমণ্ডলী লাঞ্ছিত করেছেন; এবং তার দ্বিতীয় কারণ এই যে, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রকাশ্যে লাঞ্ছনা দেবার উদ্দেশ্যেই রঙ্গমঞ্চে আনন্দ-বিদায়ের অবতারণা করেছিলেন।
দ্বিজেন্দ্রবাবু লিখেছেন যে, তিনি সকলরকম ‘মি’র বিপক্ষে। ন্যাকামি জ্যাঠামি ভণ্ডামি বোকামি প্রভৃতি যেসকল ‘মি’-ভাগান্ত পদার্থের তিনি উল্লেখ করেছেন, সেগুলির যে কোনো ভদ্রলোকেই পক্ষপাতী, এরূপ আমার বিশ্বাস নয়; অন্তত পক্ষপাতী হলেও সেকথা কেউ মুখে স্বীকার করবেন না। কিন্তু সমাজে থাকতে হলেই পাঁচটি ‘মি’ নিয়েই আমাদের ঘর করতে হয়, এবং সেই কারণেই সপরিচিত ‘মি’গুলি, সাহিত্যে না হোক, জীবনে আমাদের সকলেরই অনেকটা সওয়া আছে। কিন্তু যা আছে, তার উপর যদি একটা নতুন ‘মি’ এসে আমাদের ঘাড়ে চাপে, তাহলে সেটা নিতান্ত ভয়ের বিষয় হয়ে ওঠে। আমরা এতদিন নিরীহ প্রকৃতির লোক বলেই পরিচিত ছিলুম। কিছুদিন থেকে ষণ্ডামি নামে একটা নতুন ‘মি’ আমাদের সমাজে প্রবেশলাভ করেছে। এতদিন রাজনীতির রঙ্গভূমিতেই আমরা তার পরিচয় পেয়েছি। সরাটকনগ্রেসে সেই ‘মি’র তাণ্ডবনৃত্যের অভিনয় হয়েছিল। আমার বিশ্বাস ছিল যে, সুরাটে যে যবনিকাপতন হয়েছে, তা আর সহসা উঠবে না। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি যে, রাজনীতিতে প্রশ্রয় পেয়ে ষণ্ডামি ক্রমশ সমাজের অপরসকল দেশও অধিকার করে নিয়েছে। ষণ্ডামি-জিনিসটের আর যে ক্ষেত্রেই সার্থকতা থাক, সাহিত্যে নেই; কেননা, সাহিত্যে বাহুবলের কোনো স্থান নেই। স্টার-থিয়েটারের বক্স হতে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে গায়ের জোরে নামানো সহজ, কিন্তু তিনি বঙ্গসাহিত্যে যে উচ্চ-আসন লাভ করেছেন, বাহুবলে তাঁকে সেখান থেকে নামানো অসম্ভব। লেখকমাত্রেই নিন্দাপ্রশংসা সম্বন্ধে পরাধীন। সমালোচকদের চোখরাঙানি সহ্য করতে লেখকমাত্রেরই প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সাহিত্যজগতের ঢিলটে মারলে যে জড়জগতের পাটকেলটা আমাদের খেতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। ওরকম একটা নিয়ম প্রচলিত হলে সাহিত্যরাজ্যে আমাদের বাস করা চলবে না। কারণ একথা সৰ্ববাদিসম্মত যে, বুদ্ধির জোর গায়ের জোরের কাছে বরাবরই হার মানে। এই কারণেই শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যেভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন, তার জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত এবং লজ্জিত।
২.
কিন্তু শ্ৰীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় যে, এ যুগের সাহিত্যে আবার ‘কবির লড়াই’ ফিরে আনবার প্রয়াস পেয়েছেন, তার জন্য আমি আরও বেশি দুঃখিত। ও কাজ একবার আরম্ভ করলে শেষটা খেউড় ধরতেই হবে। দ্বিজেন্দ্রবাবু বোধ হয় একথা অস্বীকার করবেন না যে, সেটি নিতান্ত অবাঞ্ছনীয়।
এ পৃথিবীতে মানুষে আসলে খালি দুটি কার্যই করতে জানে; সে হচ্ছে হাসতে এবং কাঁদতে। আমরা সকলেই নিজে হাসতেও জানি, কাঁদতেও জানি; কিন্তু সকলেরই কিছু,আর অপরকে হাসাবার কিংবা কাঁদাবার শক্তি নেই। অবশ্য অপরকে চপেটাঘাত করে কাঁদানো কিংবা কাতুকুতু দিয়ে হাসানো আমাদের সবারই আয়ত্ত, কিন্তু সরস্বতীর বীণার সাহায্যে কেবল দুটিচারটি লোকই ঐ কার্য করতে পারেন। যাঁদের সে ভগবৎদত্ত ক্ষমতা আছে, তাঁদেরই আমরা কবি বলে মেনে নিই। বাদবাকি সব বাজে লেখক। কাব্যে, আমার মতে, শুধু তিনটিমাত্র রস আছে : করণ রস, হাস্যরস, আর হাসিকান্নামিশ্রিত মধুর রস। যে লেখায় এর একটি-না-একটি রস আছে, তাই কাব্য; বাদবাকি সব নীরস লেখা। দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদি যা খুশি তা হতে পারে, কিন্তু কাব্য নয়। বাংলাসাহিত্যে হাস্যরসে শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অদ্বিতীয়। তাঁর গানে হাস্যরস ভাবে কথায় সরে তালে লয়ে পঞ্চীকৃত হয়ে মতিমান হয়ে উঠেছে। হাসির গান তাঁর সঙ্গে জড়িতে গাইতে পারে, বঙ্গসাহিত্যের আসরে এমন গুণী আর-একটিও নেই। কান্নার মত হাসিরও নানাপ্রকার বিভিন্ন রূপে আছে, এবং দ্বিজেন্দ্রবাবুর মুখে হাসি নানা আকারেই প্রকাশ পেয়েছে। সাহিত্যে যে কেবল আমাদের মিষ্টি হাসিই হাসতে হবে, একথা আমি মানি নে। সুতরাং দ্বিজেন্দ্রবাবু যে বলেছেন যে, কাব্যে বিদ্রুপের হাসিরও ন্যায্য স্থান আছে, সেকথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু উপহাস জিনিসটের প্রাণই হচ্ছে হাসি। হাসি বাদ দিলে শুধু তার উপটুকু থাকে, কিন্তু তার রূপটকু থাকে না। হাসতে হলেই আমরা অল্পবিস্তর দন্তবিকাশ করতে বাধ্য হই। কিন্তু দন্তবিকাশ করলেই যে সে ব্যাপারটা হাসি হয়ে ওঠে তা নয়; দাঁতখিচুনি বলেও পৃথিবীতে একটা জিনিস আছে সে ক্রিয়াটি যে ঠিক হাসি নয়, বরং তার উলটো, জীবজগতে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। সুতরাং উপহাস-জিনিসটে সাহিত্যে চললেও, কেবলমাত্র তার মুখভঙ্গিটি সাহিত্যে চলে না। কোনো জিনিস দেখে যদি আমাদের হাসি পায়, তাহলেই আমরা অপরকে হাসাতে পারি। কিন্তু কেবলমাত্র যদি রাগই হয়, তাহলে সে মনোভাবকে হাসির ছদ্মবেশ পরিয়ে প্রকাশ করলে দর্শকমণ্ডলীকে শুধু রাগাতেই পারি। দ্বিজেন্দ্রবাবু এইকথাটি মনে রাখলে লোককে হাসাতে গিয়ে রাগাতেন না।
৩.
দ্বিজেন্দ্রবাবু বলেছেন যে, নাটকাকারে প্যারডি কোনো ভাষাতেই নেই। যা কোনো দেশে কোনো ভাষাতেই ইতিপূর্বে রচিত হয় নি, তাই সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি একটি অদ্ভুত পদার্থের সৃষ্টি করেছেন। বিশ্বামিত্রের তপোবল আমাদের কারও নেই; সুতরাং বিশ্বামিত্রও যখন নূতন সৃষ্টি করতে গিয়ে অকৃতকার্য হয়েছিলেন, তখন আমরা যে হব, এ তো নিশ্চিত।
মানুষে মুখ ভ্যাংচালে দর্শকমাত্রই হেসে থাকে। কেন যে সে কাজ করে, তার বিচার অনাবশ্যক; কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এই যে, ওরূপ মুখভঙ্গি দেখলে মানুষের হাসি পায়। প্যারডি হচ্ছে সাহিত্যে মুখ-ভ্যাংচানো। প্যারডি নিয়ে যে নাটক হয় না, তার কারণ দু ঘণ্টা ধরে লোকে একটানা মুখে ভেংচে যেতে পারে না; আর যদিও কেউ পারে তো, দর্শকের পক্ষে তা অসহ্য হয়ে ওঠে। হঠাৎ এক মুহূর্তের জন্য দেখা দেয় বলেই, এবং তার কোনো মানেমোন্দা নেই বলেই, মানুষের মুখ-ভ্যাংচানি দেখে হাসি পায়। সতরাং ভ্যাংচানির মধ্যে দর্শন বিজ্ঞান সনীতি সুরুচি প্রভৃতি ভীষণ জিনিস সব পুরে দিতে গেলে ব্যাপারটা মানুষের পক্ষে রুচিকর হয় না। ঐরূপ করাতে ভ্যাংচানির শুধু ধর্ম নষ্টই হয়। শিক্ষাপ্রদ ভ্যাংচানির সৃষ্টি করতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রবাবু রসজ্ঞানের পরিচয় দেন নি। যদি প্যারডির মধ্যে কোনোরূপ দর্শন থাকে তো সে দন্তের দর্শন।
৪.
দ্বিজেন্দ্রবাবু তাঁর ‘আনন্দ-বিদায়ে’র ভূমিকায় প্রকারান্তরে স্বীকারই করেছেন যে, লোকহাসানো নয়, লোকশিক্ষা দেওয়াই তাঁর মনোগত অভিপ্রায়; প্রহসন শুধু অছিলামাত্র। বেত হাতে গুরুমশাইগিরি করা, এ যুগের সাহিত্যে কোনো লোকের পক্ষেই শোভা পায় না। পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম। ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভাবামি যুগে যুগে।।—একথা শুধু অবতীর্ণ ভগবানের মুখেই সাজে, সামান্য মানবের মুখে সাজে না। লেখকেরা যদি নিজেদের এক-একটি ক্ষুদ্র অবতারস্বরূপ মনে করেন, কিংবা যদি তাঁরা সকলে কেষ্টবিষ্ট হয়ে ওঠেন, তাহলে পৃথিবীর সাধুদেরও পরিত্রাণ হবে না, এবং দুষ্টদেরও শাসন হবে না; লাভের মধ্যে লেখকেরা পরস্পর শুধু কলমের খোঁচাখুচি করবেন। দ্বিজেন্দ্রবাবুর ইচ্ছাও যে তাই হয়। এবং তিনি ঐরূপ খোঁচাখুঁচি হওয়াটা যে উচিত, তাই প্রমাণ করবার জন্যে বিলেতি নজির দেখিয়েছেন। তিনি বলেন যে, ওআর্ডসওআর্থকে ব্রাউনিং চাব্কেছিলেন, এবং ওআর্ডসওআর্থ বায়ুরন এবং শেলিকে চাব্কেছিলেন। বিলেতের কবিরা যে অহরহ পরস্পরকে চাবকা-চাবকি করে থাকেন, এ জ্ঞান আমার ছিল না।
ওআর্ডসওআর্থ সম্বন্ধে ব্রাউনিং Lost Leader নামে যে একটি ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করেন, সেটিকে কোনো হিসাবেই চাবুক বলা যায় না। কবিসমাজের সর্বমান্য এবং পূজ্য দলপতি দলত্যাগ করে অপর-দলভুক্ত হওয়াতে কবিসমাজ যে গভীর বেদনা অনুভব করেছিলেন, ঐ কবিতাতে ব্রাউনিং সেই দুঃখই প্রকাশ করেছেন। ওআর্ডসওআর্থ যে বায়ুরন এবং শেলিকে চাবকেছিলেন, একথা আমি জানতুম না। বায়ুরন অবশ্য তাঁর সমসাময়িক কবি এবং সমালোচকদের প্রতি দু হাতে ঘুঁষো চালিয়েছিলেন, কিন্তু সে আত্মরক্ষার্থ। অহিংসা পরমধর্ম হলেও আততায়ী-বধে পাপ নেই। দ্বিজেন্দ্রবাবু যে নজির দেখিয়েছেন, সেই নজিরের বলেই প্রমাণ করা যায় যে, চাবুক পদার্থটার বিলেতি কবিসমাজে চলন থাকলেও তার ব্যবহারে যে সাহিত্যের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয়েছে, তা নয়। ওআর্ডসওআর্থ শেলি বায়ুরন প্রভৃতি কোনো কবিই কোনো প্রতিদ্বন্দীর তাড়নার ভয়ে নিজের পথ ছাড়েন নি, কিংবা সাহিত্যরাজ্যে পাশ কাটিয়ে যাবারও চেষ্টা করেন নি। কবিমাত্রেরই মত যে ‘স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরঃধর্মে ভয়াবহ’। চাবুকের ভয় কেবলমাত্র তারাই করে, যাদের ‘স্বধর্ম বলে জিনিসটা আদপেই নেই এবং সাহিত্যে পরমুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। এ শ্রেণীর লেখকেরা কি লেখেন আর না-লেখেন, তাতে সমাজের কিংবা সাহিত্যের বড়-কিছু আসে যায় না।
একথা আমি অস্বীকার করি নে যে, সাহিত্যে চাবুকের সার্থকতা আছে। হাসিতে রস এবং কষ দুইই আছে। এবং ঠিক মাত্রা-অনুসারে কষের খাদ দিতে পারলে হাস্যরসে জমাট বাঁধে। কিন্তু তাই বলে ‘কষে’র মাত্রা অধিক বাড়ানো উচিত নয় যে, তাতে হাসি জিনিসটা ক্রমে অন্তর্হিত হয়ে, যা খাঁটি মাল বাকি থাকে, তাতে শুধু ‘কশাঘাত’ করা চলে। সাহিত্যেও অপরের গায়ে নাইট্রিক অ্যাসিড ঢেলে দেওয়াটা বীরত্বের পরিচয় নয়। দ্বিজেন্দ্রবাবু ‘কষাঘাত’কে ‘কশাঘাত’ বলে ভুল করে ষত্ব-ণত্ব জ্ঞানের পরিচয় দেন নি। সাহিত্যে কোনো ব্যক্তিবিশেষের উপর চাবুক প্রয়োগ করাটা অনাচার। সমগ্র সমাজের পণ্ঠেই ওর প্রয়োগটা সনাতন প্রথা। মিথ্যা যখন সমাজে আশকারা পেয়ে সত্যের সিংহাসন অধিকার করে বসে, এবং রীতি যখন নীতি বলে সম্মান লাভ করে ও সমগ্র সমাজের উপর নিজের শাসন বিস্তার করে, তখনই বিদ্রূপের দিন আসে। পৃথিবীতে সব চাপা যায়, কিন্তু হাসি চাপা যায় না। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি চাবুকের প্রয়োগ চলে না। কোনো লেখক যদি নিতান্ত অপদার্থ হয়, তাহলে তার উপর কশাঘাত করাটা কেবল নিষ্ঠুরতা; কেননা, গাধা পিটে ঘোড়া হয় না। অপরপক্ষে যদি কোনো লেখক সত্যসত্যই সরস্বতীর বরপুত্র হন, তাহলে তাঁর লেখার কোনো বিশেষ অংশ কিংবা ধরন মনোমত না হলেও, সেই বিশেষ ধরনের প্রতি যেরূপ বিদ্রূপ সংগত, সেরূপ বিদ্রূপকে আর যে নামেই অভিহিত কর, ‘চাবুক’ বলা চলে না। কারণ, ওরূপ ক্ষেত্রে কবির মর্যাদা রক্ষা না করে বিদ্রূপ করলে সমালোচকেরও আত্মমর্যাদা রক্ষিত হয় না। কোনো ফাঁক পেলেই কলি যেভাবে নলের দেহে প্রবেশ করেছিলেন, সমালোচকের পক্ষে সেইভাবে কবির দেহে প্রবেশ করা শোভনও নয়, সংগতও নয়।
৫.
চাবুক ব্যবহার করবার আর-একটি বিশেষ দোষ আছে। ও কাজ করতে করতে মানুষের খন চড়ে যায়। দ্বিজেন্দ্রবাবরও তাই হয়েছে। তিনি একমাত্র ‘চাবুকে’ সন্তুষ্ট না থেকে, ক্রমে ‘ঝাঁটিকা’ ‘চাঁটিকা’ প্রভৃতি পদার্থেরও প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেছেন। আমি বাংলায় অনাবশ্যক ‘ইকা’প্রত্যয়ের বিরোধী। সুতরাং আমি নির্ভয়ে দ্বিজেন্দ্রবাবকে এই প্রশ্ন করতে পারি যে, ‘চাঁটিকা’র ‘ইকা’ বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থাকে, সে-জিনিসটে মারাতে কি কোনো লেখকের পদমর্যাদা বৃদ্ধি পায়? ‘ঝাঁটা’ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য এই যে, সম্মার্জনীর উদ্দেশ্য ধুলোঝাড়া, গায়ের ঝালঝাড়া নয়। বিলেতিসরস্বতী মাঝেমাঝে রণচণ্ডী মতি ধারণ করলেও বঙ্গসরস্বতীর পক্ষে ঝাঁটা উঁচিয়ে রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হওয়াটা যে নিতান্ত অবাঞ্ছনীয়, একথা বোধ হয় কেউ অস্বীকার করবেন না।
৬.
শ্ৰীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নিজে মার-মতি ধারণ করবার যে কারণ দেখিয়েছেন, আমার কাছে সেটি সবচেয়ে অদ্ভুত লাগল। দ্বিজেন্দ্রবাবর মতে, যদি কোনো কবি কোনো কাব্যকে সাহিত্যের পক্ষে অমঙ্গলকর বিবেচনা করেন, তাহা হইলে সেরূপ কাব্যকে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে চাবকাইয়া দেওয়া তাঁহার কর্তব্য।
এককথায়, সাহিত্যের মঙ্গলের জন্য নৈতিক চাবুক মারাই দ্বিজেন্দ্রবাবুর অভিপ্রায়। পৃথিবীতে অনেক লোকের ধারণা যে কাউকে ধর্মাচরণ শেখাতে হলে মৃত্যুর মত তার চুল চেপে ধরাটাই তার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়, এবং সেইজন্য কর্তব্য। স্কুলে জেলখানায় ঐ সমাজের মঙ্গলের জন্যই বেত মারবার নিয়ম প্রচলিত ছিল। কিন্তু আজকাল অনেকেরই এ জ্ঞান জন্মেছে যে, ও পদ্ধতিতে সমাজের কোনো মঙ্গলই সাধিত হয় না; লাভের মধ্যে শুধু যে বেত মারে এবং যাকে মারা হয়, উভয়েই তার ফলে মনুষ্যত্ব হারিয়ে পশুত্ব লাভ করে। অপরের উপর অত্যাচার করবার জন্য শারীরিক বলের প্রয়োগটা যে বর্বরতা, একথা সকলেই মানেন; কিন্তু একই উদ্দেশ্যে নৈতিক বলের প্রয়োগটাও যে বর্বরতামাত্র, এ সত্য আজও সকলের মনে বসে যায় নি। কঠিন শাস্তি দেবার প্রবৃত্তিটি আসলে রূপান্তরে প্রতিহিংসাপ্রবত্তি। ও জিনিসটিকে সমাজের মঙ্গলজনক মনে করা শুধু নিজের মনভোলানো মাত্র। নীতিরও একটা বোকামি গোঁড়ামি এবং গণ্ডামি আছে। নিত্যই দেখতে পাওয়া যায়, একরকম প্রকৃতির লোকের হাতে নীতি-পদার্থটা পরের উপর অত্যাচার করবার একটা অমাত্র। ধর্ম এবং নীতির নামে মানুষকে মানুষে যত কষ্ট দিয়েছে, যত গহিত কার্য করেছে, এমন বোধ হয় আর কিছুরই সাহায্যে করে নি। আশা করি দ্বিজেন্দ্রবাবু সে শ্রেণীর লোক নন, যাঁদের মতে সুনীতির নামে সাত খুন মাপ হয়। ইতিহাসে এর ধারাবাহিক প্রমাণ আছে যে, নীতির বোকামি গোঁড়ামি এবং গুণ্ডামির অত্যাচার সাহিত্যকে পুরোমাত্রায় সহ্য করতে হয়েছে। কারণ, সাহিত্য সকল দেশে সকল যুগেই বোকামি গোঁড়ামি এবং গুণ্ডামির বিপক্ষ এবং প্রবল শত্র।
নীতির, অর্থাৎ যুগবিশেষে প্রচলিত রীতির, ধর্মই হচ্ছে মানুষকে বাঁধা; কিন্তু সাহিত্যের ধর্ম হচ্ছে মানুষকে মুক্তি দেওয়া। কাজেই পরস্পরের সঙ্গে দা-কুমড়োর সম্পর্ক। ধর্ম এবং নীতির দোহাই দিয়েই মুসলমানেরা আলেকজান্ড্রিয়ার লাইব্রেরি ভস্মসাৎ করেছিল।
এ যুগে অবশ্য নীতিবীরদের বাহুবলের এক্তিয়ার হতে আমরা বেরিয়ে গেছি, কিন্তু সুনীতির গোয়েন্দারা আজও সাহিত্যকে চোখে-চোখে রাখেন, এবং কারও লেখায় কোনো ছিদ্র পেলেই সমাজের কাছে লেখককে ধরিয়ে দিতে উৎসুক হন। কাব্যামৃতরসাস্বাদ করা এক, কাব্যের ছিদ্রান্বেষণ করা আর। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি কবিতার রূপকমাত্র। কারণ, সে বাঁশির ধর্মই এই যে, তা ‘মনের আকুতি বেকত করিতে কত না সন্ধান জানে’। ছিদ্রান্বেষী নীতি ধর্মীদের হাত পড়লে সে বাঁশির ফটোগুলো যে তাঁরা বাজিয়ে দিতে চেষ্টা করবেন, তাতে আর সন্দেহ কি। একশ্রেণীর লোক চিরকালই এই চেষ্টা করে অকৃতকার্য হয়েছেন; কারণ, সে ছিদ্র স্বয়ং ভগবানের হাতে-করা বিঁধ, তাকে নিরেট করে দেবার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই। ‘মি’-জিনিসটিই খারাপ, কিন্তু আমাদের শাস্ত্রমতে, মানুষের পক্ষে সবচাইতে সর্বনেশে ‘মি’ হচ্ছে ‘আমি’। কারণ, ও পদার্থটির আধিক্য থাকলে আমাদের বিদ্যাবৃদ্ধি কাণ্ডজ্ঞান সবই লুপ্ত হয়ে আসে। অন্যান্য সকল ‘মি’ ঐ ‘আমি’কে আশ্রয় করেই থাকে। কিন্তু ‘আমি’ এত অব্যক্তভাবে আমাদের সমস্ত মনটায় ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে যে, আমরা নিজেও বুঝতে পারি নে যে, তারই তাড়নায় আমরা পরের উপর কুব্যবহার করতে উদ্যত হই, সমাজ কিংবা সাহিত্য কারও মঙ্গলের জন্য নয়। এইকথাটা স্পষ্ট বুঝতে পারলে আমরা পরের উপর নৈতিক চাবুক প্রয়োগ করতে কুণ্ঠিত হই। এই কারণেই, যদি একজন কবি অপর-একজন সমসাময়িক কবির সমালোচক হয়ে দাঁড়ান, তাহলে তাঁর নিকট কবি এবং কাব্যের ভেদবুদ্ধিটি নষ্ট হওয়া অতি সহজ।
৭.
দ্বিজেন্দ্রবাবু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা হতে দুর্নীতির যে প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন, তা হাস্যরসাত্মক না হোক, হাস্যকর বটে। ‘কেন যামিনী না যেতে জাগালে না’–একথাটা ভারতবাসীর পক্ষে যে অপ্রীতিকর, তা আমি স্বীকার করতে বাধ্য; কেননা, যামিনী গেলেও আমরা জাগবার বিপক্ষে। আমরা শুধু রাতে নয়, অষ্টপ্রহর ঘুমতে চাই। সুতরাং যদি কেউ অন্ধকারের মধ্যেই চোখ খোলবার পক্ষপাতী হন, তাহলে তাঁর উপর বিরক্ত হওয়া আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। সে যাই হোক, ও গানটিতে বঙ্গসাহিত্যের যে কি অমঙ্গল ঘটেছে, তা আমি বুঝতে পারলাম না। এদেশের কাব্যরাজ্যে অভিসার বহুকাল হতে প্রচলিত আছে। রাধিকার নামে বেনামি করলে ও কবিতাটি সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রবাবুর বোধ হয় আর-কোনো আপত্তি থাকত না। আমরা যে নাম-জিনিসটির এতটা অধীন হয়ে পড়েছি, সেটা আমাদের পক্ষে মোটেই শ্লাঘার বিষয় নয়। আর যদি দ্বিজেন্দ্রবাবুর মতে ও গানটি ভদ্রসমাজে অশ্রাব্য হয়, তাহলে সেটির প্যারডি করে তিনি কি তাকে এতই সুশ্রাব্য করে তুলেছেন যে, সেটি রঙ্গালয়ে চীৎকার করে না গাইলে আর সমাজ উদ্ধার হয় না? দ্বিজেন্দ্রবাবু যেমন বিলেতি নজিরের বলে চাবকা-চাবকি বঙ্গসাহিত্যে প্রচলিত করতে চেয়েছেন, তেমনি তিনি আমাদের সাহিত্যে বিলেতি puritanismএর ভূত নামাতে চান। ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের অনেক ত্রুটি আছে, কিন্তু puritanism-নামক ন্যাকামি এবং গোঁড়ামি হতে এদেশীয় সাহিত্য চিরকালই মুক্ত ছিল। দ্বিজেন্দ্রবাবুর মত যদি আমাদের গ্রাহ্য করতে হয়, তাহলে অশ্বঘোষের ‘বুদ্ধচরিত’ থেকে শুরু করে জয়দেবের ‘গীতগোবিন্দ’ পর্যন্ত অন্তত হাজার বৎসরের সংস্কৃতকাব্যসকল আমাদের অগ্রাহ্য করতে হবে; একখানিও টিকবে না। তারপর বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস থেকে আরম্ভ করে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত সকল কবির সকল গ্রন্থই আমাদের অস্পৃশ্য হয়ে উঠবে; একখানিও বাদ যাবে না। যাঁরা রবীন্দ্রবাবুর সরস্বতীর গাত্রে কোথায় কি তিল আছে তাই খুঁজে বেড়ান, তাঁরা যে ভারতবর্ষের পূর্বকবিদের সরস্বতীকে কি করে তুষারগৌরীরূপে দেখেন, তা আমার পক্ষে একেবারেই দুর্বোধ্য। শেষ কথা, puritanismএর হিসেব থেকে স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রবাবুও কিছু কম অপরাধী নন। তার প্রমাণ তো হাতে-হাতেই রয়েছে। ‘আনন্দ-বিদায়’ moral text-book বলে গ্রাহ্য হবে, এ আশা যদি তিনি করে থাকেন, তাহলে সে আশা সফল হবে না।
মাঘ ১৩১৯
সুরের কথা
আপনারা দেশী বিলেতি সংগীত নিয়ে যে বাদানুবাদের সৃষ্টি করেছেন, সে গোলযোগে আমি গলাযযাগ করতে চাই।
এবিষয়ে বক্তৃতা করতে পারেন এক তিনি, যিনি সংগীতবিদ্যার পারদশী; আর-এক তিনি, যিনি সংগীতশাস্ত্রের সারদর্শী অর্থাৎ যিনি সংগীত সম্বন্ধে হয় সর্বজ্ঞ, নয় সর্বজ্ঞ। আমি শেষোক্ত শ্রেণীর লোক, অতএব এবিষয়ে আমার কথা বলবার অধিকার আছে।
আপনাদের সুরের আলোচনা থেকে আমি যা সার সংগ্রহ করেছি সংক্ষেপে তাই বিবত করতে চাই। বলা বাহুল্য, সংগীতের সুর ও সার পরস্পর পরস্পরের বিরোধী। এর প্রথমটি হচ্ছে কানের বিষয়, আর দ্বিতীয়টি জ্ঞানের। আমরা কথায় বলি সরসার, কিন্তু সে দ্বন্দ্বসমাস হিসেবে।
সব বিষয়েরই শেষকথা তার প্রথমকথার উপরেই নির্ভর করে; যে বস্তুর আমরা আদি জানি নে, তার অন্ত পাওয়া ভার। অতএব কোনো সমস্যার চড়ান্ত মীমাংসা করতে হলে তার আলোচনা ক-খ থেকে শুরু করাই সনাতন পদ্ধতি; এবং এক্ষেত্রে আমি সেই সনাতন পদ্ধতিই অনুসরণ করব।
অবশ্য একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এমন লোক ঢের আছে যারা দিব্যি বাংলা বলতে পারে অথচ ক-খ জানে না; আমাদের দেশের বেশির ভাগ স্ত্রী-পুরুষই তো ঐ দলের। অপরপক্ষে, এমন প্রাণীরও অভাব নেই, যারা ক-খ জানে অথচ বাংলা ভালো বলতে পারে না— যথা আমাদের ভদ্রশিশুর দল। অতএব এরূপ হওয়াও আশ্চর্য নয় যে— এমন গুণী ঢের আছে, যারা দিব্যি গাইতে-বাজাতে পারে অথচ সংগীতশাস্ত্রের ক-খ জানে না; অপরপক্ষে এমন জ্ঞানীও ঢের থাকতে পারে, যারা সংগীতের শুধু ক-খ নয় অনুঘরবিসর্গ পর্যন্ত জানে, কিন্তু গানবাজনা জানে না।
তবে যারা গানবাজনা জানে, তারা গায় ও বাজায়; যারা জানে না, তারা ও-বস্তু নিয়ে তর্ক করে। কলধনি না করতে পারি, কলরব করবার অধিকার আমাদের সকলেরই আছে। সুতরাং এই তকে যোগ দেওয়াটা আমার পক্ষে অনধিকারচর্চা হবে না। অতএব আমাকে ক-খ থেকেই শুরু করতে হবে, অ-আ থেকে নয়। কেননা, আমি যা লিখতে বসেছি, সে হচ্ছে সংগীতের ব্যঞ্জনলিপি, স্বরলিপি নয়। আমার উদ্দেশ্য সংগীতের তত্ত্ব ব্যক্ত করা, তার স্বত্ব সাব্যস্ত করা নয়। আমি সংগীতের সারদর্শী, সুরস্পর্শী নই।
২.
হিন্দুসংগীতের ক-খ-জিনিসটে কি?–বলছি।
আমাদের সকল শাস্ত্রের মুল যা, আমাদের সংগীতেরও মূল তাই–অর্থাৎ শ্রুতি।
শুনতে পাই, এই শ্রুতি নিয়ে সংগীতাচার্যের দল বহুকাল ধরে বহু বিচার করে আসছেন, কিন্তু আজ-তক, এমন-কোনো মীমাংসা করতে পারেন নি, যাকে ‘উত্তর’ বলা যেতে পারে অর্থাৎ যার আর উত্তর নেই।
কিন্তু যেহেতু আমি পণ্ডিত নই, সে কারণ আমি ওবিষয়ের একটি সহজ মীমাংসা করেছি, যা সহজ মানুষের কাছে সহজে গ্রাহ্য হতে পারে।
আমার মতে শ্রুতির অর্থ হচ্ছে সেই ঘর, যা কানে শোনা যায় না; যেমন দর্শনের অর্থ হচ্ছে সেই সত্য, যা চোখে দেখা যায় না। যেমন দর্শন দেখবার জন্য দিব্যচক্ষু, চাই, তেমনি শ্ৰতি শোনবার জন্য দিব্যকণ চাই। বলা বাহুল্য, তোমার-আমার মত সহজ মানুষদের দিব্যচক্ষুও নেই, দিব্যকণও নেই; তবে আমাদের মধ্যে কারও কারও দিব্যি চোখও আছে, দিব্যি কানও আছে। ওতেই তো হয়েছে মুশকিল। চোখ ও কান সম্বন্ধে দিব্য এবং দিব্যি— এ দুটি বিশেষণ, কানে অনেকটা এক শোনালেও মানেতে ঠিক উলটো।
সংগীতে যে সাতটি শাদা আর পাঁচটি কালো সুর আছে, এ সত্য পিয়ানো কিংবা হারমোনিয়ামের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে সকলেই দেখতে পাবেন। এই পাঁচটি কালো সুরের মধ্যে যে, চারটি কোমল আর একটি তীব্র তা আমরা সকলেই জানি এবং কেউ-কেউ তাদের চিনিও। কিন্তু চেনাশনোজিনিসে পণ্ডিতের মনস্তুষ্টি হয় না। তাঁরা বলেন যে, এদেশে ঐ পাঁচটি ছাড়া আরও কালো এবং এমন কালো সুর আছে, যেমন কালো বিলেতে নেই। শাস্ত্রমতে সেসব হচ্ছে অতিকোমল ও অতিতীব্র। ঐ নামই প্রমাণ যে, সেসব অতীন্দ্রিয় সুর এবং তা শোনবার জন্যে দিব্যকর্ণ চাই–যা তোমার-আমার তো নেই, শাস্ত্রীমহাশয়দেরও আছে কি না সন্দেহ। আমার বিশ্বাস, তাঁদেরও নেই। শ্ৰতি সেকালে থাকলেও একালে তা স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে। স্মৃতিই যে শ্ৰতিধরদের একমাত্র শক্তি, এ সত্য তো জগদ্বিখ্যাত। সুতরাং একথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, সংগীত সম্বন্ধে পরের মুখে ঝাল খাওয়া, অর্থাৎ পরের কানে মিষ্টি শোনা, যাঁদের অভ্যাস শুধু তাঁদের কাছেই শ্রুতি এতিমধুর। আমি স্থির করেছি যে, আমাদের পক্ষে ঐ বারোই ভালো; অবশ্য সাতপাঁচ ভেবেচিন্তে। ও দ্বাদশকে ছাড়াতে গেলে, অর্থাৎ ছাড়লে, আমাদের কানকে একাদশী করতে হবে।
আর ধরুন, যদি ঐ দ্বাদশ সরের ফাঁকে ফাঁকে সত্যসত্যই শ্ৰতি থাকে, তাহলে সেসব স্বর হচ্ছে অনুঘর। সা- এবং নি-র অন্তর্ভূত দশটি সুরের গায়ে যদি কোনো অসাধারণ পণ্ডিত দশটি অনুঘর জুড়ে দিতে পারেন, তাহলে সংগীত এমনি সংস্কৃত হয়ে উঠবে যে, আমাদের মত প্রাকৃতজনেরা তার এক বর্ণও বুঝতে পারবে না।
৩.
এসব তো গেল সংগীতের বর্ণপরিচয়ের কথা, শব্দবিজ্ঞানের নয়। শব্দেরও যে একটা বিজ্ঞান আছে, এ জ্ঞান সকলের নেই। সুতরাং সরের। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব গ্রাহ্য না হলেও আলোচ্য।
শব্দজ্ঞানের মতে শ্রুতি অপৌরুষেয়; অর্থাৎ স্বরগ্রাম কোনো পুরুষ কতৃক রচিত হয় নি, প্রকৃতির বক্ষ থেকে উত্থিত হয়েছে। একটি একটানা তারের গায়ে ঘা মারলে প্রকৃতি অমনি সাত-সরে কেঁদে ওঠেন। এর থেকে বৈজ্ঞানিকেরা ধরে নিয়েছেন যে, প্রকৃতি তাঁর একতারায় যে সকাতর সাগম আলাপ করেন, মানুষে শুধু তার নকল করে। কিন্তু সে নকলও মাছিমারা হয় না। মানুষের গলগ্রহ কিংবা যন্ত্রস্থ হয়ে প্রকৃতিদত্ত স্বরগ্রামের কোনো সুর একটু চড়ে, কোনো সুর একটু ঝুলে যায়। তা তো হবারই কথা। প্রকৃতির হদয়তলী থেকে এক ঘায়ে যা বেরয়, তা যে একঘেয়ে হবে–এ তো স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং মানুষে এইসব প্রাকৃত সরকে সংস্কৃত করে নিতে বাধ্য।
এ মত লোকে সহজে গ্রাহ্য করে; কেননা, প্রকৃতি যে একজন মহা ওস্তাদ— এ সত্য লৌকিক ন্যায়েও সিদ্ধ হয়। প্রকৃতি অন্ধ, এবং অন্ধের সংগীতে বৎপত্তি যে সহজ, এ সত্য তো লোকবিশ্রত।
প্রকৃতির ভিতর যে শব্দ আছে শুধু শব্দ নয়, গোলযোগ আছেএকথা সকলেই জানেন; কিন্তু তাঁর গলায় যে সুর আছে, একথা সকলে মানেন না। এই নিয়েই তো আট ও বিজ্ঞানে বিরোধ।
আর্টিস্টরা বলেন, প্রকৃতি শুধু অন্ধ নন, উপরন্তু বধির। যাঁর কান নেই, তাঁর কাছে গানও নেই। সাংখ্যদর্শনের মতে পুরুষ দ্রষ্টা এবং প্রকৃতি নর্তকী; কিন্তু প্রকৃতি যে গায়িকা এবং পুরুষ শ্রোতা–একথা কোনো দর্শনেই বলে না। আর্টিস্টদের মতে তৌত্রিকের একটিমাত্র অঙ্গ-নৃত্যই প্রকৃতির অধিকারভুক্ত, অপর দুটি— গীত বাদ্য— তা নয়।
এর উত্তরে বিজ্ঞান বলেন, এ বিশ্বের সকল রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের উপাদান এবং নিমিত্তকারণ হচ্ছে ঐ প্রকৃতির নত্য। কথাটা উড়িয়ে দেওয়া চলে না, অতএব পুড়িয়ে দেখা যাক ওর ভিতর কতটুকু খাঁটি মাল আছে।
শাস্ত্রে বলে, শব্দ আকাশের ধর্ম; বিজ্ঞান বলে, শব্দ আকাশের নয় বাতাসের ধর্ম। আকাশের নত্য অর্থাৎ সর্বাগের স্বচ্ছন্দ কম্পন থেকে যে আলোকের, এবং বাতাসের উত্তরপ কম্পন থেকে যে ধনির উৎপত্তি হয়েছেতা বৈজ্ঞানিকেরা হাতে-কলমে প্রমাণ করে দিতে পারেন। কিন্তু আর্ট বলে, আত্মার কম্পন থেকে সরের উৎপত্তি, সতরাং জড়প্রকৃতির গভে তা জন্মলাভ করে নি। আত্মা কাঁপে আনন্দে, সৃষ্টির চরম আনন্দে; আর আকাশ-বাতাস কাঁপে বেদনায়, সৃষ্টির প্রসববেদনায়। সুতরাং আর্টিস্টদের মতে সুর শব্দের অনুবাদ নয়, প্রতিবাদ।
যেখানে আটে ও বিজ্ঞানে মতভেদ হয়, সেখানে আপোস-মীমাংসার জন্য দর্শনকে সালিশ মানা ছাড়া আর উপায় নেই। দার্শনিকেরা বলেন, শব্দ হতে সুরের কিংবা সুর হতে শব্দের উৎপত্তি— সে বিচার করা সময়ের অপব্যয় করা। এস্থলে আসল জিজ্ঞাস্য হচ্ছে, রাগ ভেঙে সুরের, না সুর জুড়ে রাগের সৃষ্টি হয়েছে এককথায়, সর আগে না রাগ আগে। অবশ্য রাগের বাইরে সাগমের কোনো অস্তিত্ব নেই, এবং সাগমের বাইরে রাগের কোনো অস্তিত্ব নেই। সুতরাং সর পর্বরাগী কি অনুরাগী, এই হচ্ছে আসল সমস্যা। দার্শনিকেরা বলেন যে, এ প্রশ্নের উত্তর তাঁরাই দিতে পারেন যাঁরা বলতে পারেন বীজ আগে কি বক্ষ আগে; অর্থাৎ কেউ পারেন না।
আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, উক্ত দার্শনিক সিদ্ধান্তের আর-কোনো খণ্ডন নেই। তবে বক্ষায়ুর্বেদীরা নিশ্চয়ই বলবেন যে, বক্ষ আগে কি বীজ আগে, সে রহস্যের ভেদ তাঁরা বালাতে পারেন। কিন্তু তাতে কিছু আসেযায় না। কেননা, ওকথা শোনবামাত্র আর-এক দলের বৈজ্ঞানিক, অর্থাৎ পরমাণবাদীরা, জবাবু দেবেন যে সংগীত আয়ুর্বেদের নয় বায়ুর্বেদের অন্তর্ভূত; অর্থাৎ বিজ্ঞানের বিষে বিষক্ষয় হয়ে যাবে।
আসল কথা এই যে, আমি কর্তা তুমি ভোত্তা এ জ্ঞান যার নেই, তিনি আর্টিস্ট নন। সুতরাং সংগীত সম্বন্ধে প্রকৃতিকে সম্বােধন করে— তুমি কর্তা আমি ভোক্তা–একথা কোনো আর্টিস্ট কখনো বলতে পারবেন না, এবং ওকথা মুখে আনবার কোনো দরকারও নেই। প্রকৃতির হাতে-গড়া এই বিশ্বসংসার যে আগাগোড়া বেসুরো, তার অকাট্য প্রমাণ আমরা পৃথিবীসদ্ধ লোক পৃথিবী ছেড়ে সরলোকে যাবার জন্য লালায়িত।
অতএব দাঁড়াল এই যে, সংগীতের উৎপত্তির আলোচনায় তার লয়ের সম্ভাবনাই বেড়ে যায়। তাই সহজ মানুষে চায় তার স্থিতি, ভিত্তি নয়।
৪.
অতঃপর দেশী বিলেতি সংগীতের ভেদাভেদ নির্ণয় করবার চেষ্টা করা যাক।
।এ দুয়ের মধ্যে আর যা প্রভেদই থাক, তা অবশ্য ক-খ-গত নয়। যে বারো সরে এদেশের সংগীতের মূলধন, সেই বারো সুরই যে সেদেশের সংগীতের মূলধন–একথা সর্ববাদিসম্মত। তবে আমরা বলি যে, সে মূলধন আমাদের হাতে সদে বেড়ে গিয়েছে। আমাদের হাতে কোনো ধন যে সুদে বাড়ে, তার বড়-একটা প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাছাড়া আমি পূর্বে দেখিয়েছি যে, সরের এই অতিসদের লোভে আমরা সংগীতের মূলধন হারাতে বসেছি। সুতরাং এবিষয়ে আর বেশিকিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।
দেশীর সঙ্গে বিলেতি সংগীতের আসল প্রভেদটা ক-খ নিয়ে নয়, করখল নিয়ে। BLA=ব্লে –CLA=ক্লের সঙ্গে কর-খলের, কানের দিক থেকেই হোক আর মানের দিক থেকেই হোক, একটা-যে প্রকাণ্ড প্রভেদ আছে— এ হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড সত্য। এ প্রভেদ উপাদানের নয়, গড়নের। অতএব রাগ ও মেলডির ভিতর পার্থক্য হচ্ছে ব্যাকরণের, এবং একমাত্র ব্যাকরণেরই।
সুতরাং আমরা যদি বিলেতি ব্যাকরণ অনুসারে সুর সংযোগ করি তাহলে তা রাগ না হয়ে মেলডি হবে, এবং তাতে অবশ্য রাগের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। আমরা ইংরেজি ব্যাকরণ অনুসারে ইংরেজিভাষা লিখলে সে লেখা ইংরেজিই হয়, এবং তাতে বাংলাসাহিত্যের কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, যদিচ এক্ষেত্রে শুধু ব্যাকরণ নয় শব্দও বিদেশী। কিন্তু যেমন কতকটা ইংরেজি এবং কতকটা বাংলা ব্যাকরণ মিলিয়ে, এবং সেইসঙ্গে বাংলা শব্দের অনুবাদের গোঁজামিলন দিলে, তা বাবু ইংলিশ হয়, এবং উক্ত পদ্ধতি অনুসারে বাংলা লিখলে তা সাধুভাষা হয় তেমনি ঐ দুই ব্যাকরণ মেলাতে বসলে সংগীতেও আমরা রাগ-মেলডির একটি খিচুড়ি পাকাব। সাহিত্যের খিচুড়িভোগে যখন আমার রুচি নেই, তখন সংগীতের ও-ভোগ যে আমি ভোগ করতে চাই নে, সেকথা বলাই বাহুল্য।
৫.
দেশী বিলেতি সংগীতের মধ্যে আর-একটা স্পষ্ট প্রভেদ আছে। বিলেতি সংগীতে হারমনি আছে, আমাদের নেই।
এই হারমনি-জিনিসটে ঘরের যুক্তাক্ষর বই আর-কিছুই নয়, অর্থাৎ ও-বস্তু হচ্ছে সংগীতের বর্ণপরিচয়ের দ্বিতীয়ভাগের অধিকারে। আমাদের সংগীত এখনও প্রথমভাগের দখলেই আছে। আমাদের পক্ষে সংগীতের দ্বিতীয়ভাগের চর্চা করা উচিত কি না, সেবিষয়ে কেউ মনস্থির করতে পারেন নি। অনেকে ভয় পান যে, দ্বিতীয়ভাগ ধরলে তাঁরা প্রথমভাগ ভুলে যাবেন। তা ভুলন আর না-ভুলন, তাঁরা যে প্রথমভাগকে আর আমল দেবেন না, সেবিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই। আমাদের সাহিত্য থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, একবার যুক্তাক্ষর শিখলে আমরা অযুক্তাক্ষরের ব্যবহার যুক্তিযুক্ত মনে করি নে এবং অপর-কেউ করতে গেলে অমনি বলে উঠি, সাহিত্যের সর্বনাশ হল, ভাষাটা একদম অসাধ এবং অশদ্ধ হয়ে গেল। তবে সংগীতে এ বিপদ ঘটবার বিশেষ সম্ভাবনা নেই। সেদিন একজন ইংরেজ বলছিলেন যে, যে সংগীতে ছয়টি রাগ এবং প্রতি রাগের ছয়টি করে স্ত্রী আছে, সেখানে হারমনি কি করে থাকতে পারে। আমি বলি, ও তো ঠিকই কথা, বিশেষত স্বামী যখন মতিমান রাগ আর স্ত্রীরা প্রত্যেকেই এক-একটি মতিমতী রাগিণী। অবশ্য এরূপ হবার কারণ আমাদের সংগীতের কৌলিন্য। আমাদের রাগসকল যদি কুলীন না হত, তাহলেও আমরা হারমনির চর্চা করতে পারতুম না; কেননা, ও-বস্তু আমাদের ধাতে নেই। আমাদের সমাজের মত আমাদের সংগীতেও জাতিভেদ আছে, আর তার কেউ আরকারও সঙ্গে মিশ্রিত হতে পারে না। মিশ্রিত হওয়া দূরে থাক, আমরা পরস্পর পরস্পরকে স্পর্শ করতে ভয় পাই; কেননা, জাতির ধর্মই হচ্ছে জাত বাঁচিয়ে মরা। আর মিলে-মিশে এক হয়ে যাবার নামই হচ্ছে হারমনি।
পৌষ ১৩২৩
হালখাতা
আজ পয়লা বৈশাখ। নূতন বৎসরের প্রথম দিন অপর দেশের অপর জাতের পক্ষে আনন্দ-উৎসবের দিন। কিন্তু আমরা সেদিন চিনি শুধু হালখাতায়। বছরকার দিনে আমরা গত বৎসরের দেনাপাওনা লাভলোকসানের হিসেবনিকেশ করি, নূতন খাতা খুলি, এবং তার প্রথম পাতায় পুরনো খাতার জের টেনে আনি।
বৎসরের পর বৎসর যায়, আবার বৎসর আসে; কিন্তু আমাদের নূতন খাতায় কিছু নূতন লাভের কথা থাকে না। আমরা এক হালখাতা থেকে আর-এক হালখাতায় শুধু লোকসানের ঘরটা বাড়িয়ে চলেছি। এভাবে আর কিছুদিন চললে যে আমাদের জাতকে দেউলে হতে হবে, সেবিষয়ে সন্দেহ নেই। লাভের দিকে শূন্য ও লোকসানের দিকে অঙ্ক ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে, তবে আমরা ব্যাবসা গুটিয়ে নিই নে, কেন। কারণ ভবের হাটে দোকানপাট কেউ স্বেচ্ছায় তোলে না, তার উপর আবার আশা আছে। লোকে বলে, আশা না মূলে যায় না।
আমরা স্বজাতি সম্বন্ধে যে একেবারেই উদাসীন, তা নয়। গেল বৎসর, জাতিহিসেবে কায়স্থ বড় কি বৈদ্য বড়, এই নিয়ে একটা তর্ক ওঠে। যেহেতু আমরা অপরের তুলনায় সকল হিসেবেই ছোট, সেইজন্য আমাদের নিজেদের মধ্যে কে ছোট কে বড়, এ নিয়ে বিবাদবিসম্বাদ করা ছাড়া আর উপায় নেই। নিজেকে বড় বলে পরিচয় দেবার মায়া আমরা ছাড়তে পারি নে। কায়স্থ বলেন, আমি বড়; বৈদ্য বলেন, আমি বড়। শাস্ত্রে যখন নানা মুনির নানা মত, তখন সক্ষম বিচার করে এবিষয়ে ঠিকটা সাব্যস্ত করা প্রায় অসম্ভব। বৈদ্যের ব্যবসায় চিকিৎসা প্রাণরক্ষা করা; ক্ষত্রিয়ের ব্যবসায় প্রাণবধ করা। অতএব ক্ষত্রিয় নিঃসন্দেহ বৈদ্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং বৈদ্য অপেক্ষা বড় হতে গেলে ক্ষত্রিয় হওয়া আবশ্যক, এই মনে করে জনকতক কায়স্থসমাজের দলপতি ক্ষত্রিয় হবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। এ শুভসংবাদ শুনে আমি একটু বিশেষ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলুম।
কারণ, প্রথমত আমি উন্নতির পক্ষপাতী; কোনো লোকবিশেষ কিংবা জাতিবিশেষ আপন চেষ্টায় আপনার অবস্থার উন্নতি করতে উদ্যোগী হয়েছে দেখলে কিংবা শুনলে খুশি হওয়া আমার পক্ষে স্বাভাবিক। বিশেষত বাংলার পক্ষে যখন জিনিসটে এতটা নূতন। নূতনের প্রতি মন কার না যায়, অন্তত দুদণ্ডের জন্যও। অবনতির জন্য কাউকেই আয়াস করতে হয় না। ও একটু ঢিলে দিলে আপনা হতেই হয়। জড়পদার্থের প্রধান লক্ষণ। নিশ্চেষ্টতা, আর জড়পদার্থের প্রধান ধর্ম অধোগতি–গ্র্যাভিটেশন। সম্প্রতি প্রোফেসর জে সি বোস, শুনতে পাই, বৈজ্ঞানিকসমাজে প্রমাণ করেছেন যে, জড়ে ও জীবে আমাদের ভেদজ্ঞান শুধু ভ্রান্তিমাত্র। সে ভ্রান্তির মূল আমাদের চর্মচক্ষুর স্থূলদৃষ্টি। তিনি ইলেকট্রিসিটির আলোকের সাহায্যে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, অবস্থা অনুসারে জড়পদার্থের ভাবভঙ্গি ঠিক সজীব পদার্থের অনুরূপ। প্রোফেসর বোস নিজে বলেন যে, ভারতবাসীর পক্ষে এ কিছু নতুন সত্য বা তথ্য নয়; এ সত্য আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছে বহুপূর্বে ধরা পড়েছিল, তাঁদের দিব্য চক্ষু এড়িয়ে যেতে পারে নি; এককথায় এটা আমাদের খানদানী সত্য। আমি বলি, তার আর সন্দেহ কি। এ সত্যের প্রমাণের জন্য বিজ্ঞানের সাহায্যও আবশ্যক নয়, এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছেও যাবার দরকার নেই। আমরা প্রতিদিনের ও সমগ্র জীবনের কাজে নিত্য প্রমাণ দিচ্ছি যে, আমাদের দেশে জড়ে ও জীবে কোনো প্রভেদ নেই। সুতরাং কেউ যদি কার্যত ওর উলটোটা প্রমাণ করতে উদ্যত হয়, তাহলে নূতন জীবনের স্মৃতির একটু আভাস পাওয়া যায়।
আমাদের বাঙালিজাতির চিরলজ্জার কথা, আমাদের দেশে ক্ষত্রিয় নেই। এর জন্য আমরা অপর বীরজাতির ধিক্কার লাঞ্ছনা গঞ্জনা চিরকাল নীরবে সহ্য করে আসছি। ঘোষ বোস মিত্র দে দত্ত গুহ প্রভৃতিরা যে আমাদের এই চিরদিনের লজ্জা দূর, এই চিরদিনের অভাব মোচন করবার জন্য কোমর বেধেছিলেন, তার জন্য তাঁরা স্বদেশহিতৈষী ও স্বজাতিপ্রিয় লোকমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, কায়স্থেরা ক্ষত্রিয় হবার জন্য ঠিক পথটা অবলম্বন করেন নি, কাজেই অকৃতকার্য হয়েছেন। তাঁদের প্রথম ভুল, শাস্ত্রের প্রমাণের উপর নির্ভর করতে যাওয়া। কি ছিলুম সেইটে স্থির করতে হলে পুরনো পাঁজিপথি খুলে বসা আবশ্যক, কিন্তু কি হব তা স্থির করতে হলে ইতিহাসের সাহায্য অনাবশ্যক। ভবিষ্যতের বিষয় অতীত কি সাক্ষি দেবে? বিশেষত বিষয়টা হচ্ছে যখন ক্ষত্রিয় হওয়া, তখন গায়ের জোরই যথেষ্ট। কিন্তু আমাদের এমনি অভ্যাস খারাপ হয়েছে যে, আমরা শাস্ত্রের দোহাই না দিয়ে একপদও অগ্রসর হতে পারি নে।
পৃথিবীতে মানুষের উপর মানুষ অত্যাচার করবার জন্য দুটি মারাত্মক জিনিসের সৃষ্টি করেছে, অস্ত্রশস্ত্র ও শাস্ত্র। আমরা অত্যন্ত নিরীহ, কারও সঙ্গে মুখে ছাড়া ঝগড়াবিবাদ করি নে, যেখানে লড়াই হচ্ছে সে পাড়া দিয়ে হাঁটি নে— এই উপায়ে যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্রকে বেবাক ফাঁকি দিয়েছি। যা-কিছু বাকি আছে ডাক্তারের হাতে। আমরা চিররগ্ণ, সুতরাং ডাক্তারকে ছেড়ে আমরা ঘর করতে পারি নে এই উভয়সংকটে আমরা হোমিওপ্যাথি ও কবিরাজির শরণাপন্ন হয়ে সে অস্ত্রশস্ত্রেরও সংস্পর্শ এড়িয়েছি। আমাদের যখন এত বুদ্ধি, তখন শাস্ত্রের হাত থেকে উদ্ধার পাই, এমন কি কিছু উপায় বার করতে পারি নে?
কিন্তু ক্ষত্রিয় হওয়া কায়স্থের কপালে ঘটল না। রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব একে কায়স্থের দলপতি, তার উপর আবার গোষ্ঠীপতি, সুতরাং তিনি যখন এ ব্যাপারে বিরোধী হলেন তখন অপরপক্ষ ভয়ে নিরস্ত হলেন। যাঁরা ক্ষত্রিয় হতে উদ্যত, তাঁদের ভয় জিনিসটে যে আগে হতেই ত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক, একথা বোঝা উচিত ছিল। ভারত ও ক্ষাত্রধর্ম যে একসঙ্গে থাকতে পারে না, একথা বোধ হয় তাঁরা অবগত ছিলেন না। তবে হয়ত মনে করেছিলেন, যখন মুখে ব্রাহ্মণে দেশ ছেয়ে গেছে, তখন ভীরু ক্ষত্রিয়ে আপত্তি কি। জড়পদার্থেরও একটা অন্তর্নিহিত শক্তি আছে, তার কার্য হচ্ছে চলৎশক্তি রহিত করা। আমাদের সমাজকে যে নাড়ানো যায় না, তার কারণ এই জড়শক্তিই আমাদের সমাজে সর্বজয়ী শক্তি।
রাজা বিনয়কৃষ্ণ যে কায়স্থসমাজের সংস্কারের উদ্যোগে বাধা দিয়েছেন শুধু তাই নয়, তিনি এবার সমগ্র ভারতবর্ষের জাতীয় সমাজসংস্কার-মহাসভার সভাপতির আসন থেকে এই মত ব্যক্ত করেছেন যে, হিন্দুসমাজে অনেক দোষ থাকতে পারে, এবং সে দোষ না থাকলে সমাজের উপকার হতে পারে, অতএব সমাজসংস্কারের চেষ্টা করা অকর্তব্য। সমাজের সৃষ্টি ও গঠন হয়েছে অতীতে, সুতরাং তার সংস্কার ও পরিবর্তন হবে ভবিষ্যতে; বর্তমানের কোনো কর্তব্য নেই, কোনো দায়িত্ব নেই। সমাজ গড়ে মানুষে, ইচ্ছে করলে ভাঙতে পারে মানুষে; অতএব মানুষে তার সংস্কার করতে পারে না, সে ভার সময়ের হাতে, অন্ধ প্রকৃতির হাতে। এ মত যে অস্বীকার করে, সে বার্ক পড়ে নি।
আজকাল একশ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা সমাজের অবস্থা, দেশের অবস্থা, নিজেদের অবস্থা এইসব বিষয়েই একটু-আধটু চিন্তা করে থাকেন এবং শেষে এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হন যে, সাবধানের মার নেই। এরা সব জিনিসই ধীরেসুখে ঠাণ্ডাভাবে করবার পক্ষপাতী। এরা রোখ করে সম্মুখে এগতে চান না বলে কেউ যেন মনে না ভাবেন যে এরা পিছনে ফিরতে চান। যেখানে আছি সেখানে থাকাই এরা বুদ্ধির কাজ মনে করেন। বরং একটু অগ্রসর হওয়াই এরা অনুমোদন করেন, কিন্তু সে বড় আস্তে বড় সন্তর্পণে। যে হাড়বাঙালিভাব অধিকাংশ লোকের ভিতর অব্যক্তভাবে আছে, এরা কেউ কেউ পরিষ্কার সুন্দর ইংরেজিতে তা ব্যক্ত করেন। সংক্ষেপে এদের বক্তব্য এই যে, জীবনের গাধাবোট উন্নতির ক্ষীণ স্রোতে ভাসাও, সে একটু-একটু করে অগ্রসর হবে, যদিচ চোখে দেখতে মনে হবে চলছে না। কিন্তু খবরদার, লগি মেরো না, দাঁড় ফেলো না, গুন টেনো না, পাল খাটিয়ে না— শুধু চুপটি করে হালটি ধরে বসে থেকো। এই মতের নাম হচ্ছে বিজ্ঞতা। বিজ্ঞতার আমাদের দেশে বড় আদর, বড় মান্য। গাধাবোট চলে দেখে লোকে মনে করে না-জানি তাতে কত অগাধ মাল বোঝাই আছে।
বিজ্ঞতা-জিনিসটে আমাদের বর্তমান অবস্থার একটা ফল মাত্র। এ অবস্থাকে ইংরেজিতে বলে–transition period, অর্থাৎ এখন আমাদের জাতির বয়ঃসন্ধি উপস্থিত। বিদ্যাপতি ঠাকুর বয়ঃসন্ধির এই বলে বর্ণনা করেছেন যে ‘লখইতে না পার জেঠ কি কনেঠ’–এ জ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ চেনা যায় না। কাজেই আমরা কাজে ও কথায় পরিচয় দিই হয় ছেলেমির, নয় জ্যাঠামির, নাহয় একসঙ্গে দুয়ের। এই জ্যাঠাছেলের ভাবটা আমাদের বিশেষ মনঃপত। ছোটছেলের দুরন্ত ভাব আমরা মোটেই ভালোবাসি নে। তার মুখে পাকা-পাকা কথা শোনাই আমাদের পছন্দসই। এই জ্যাঠামিরই ভদ্র নাম বিজ্ঞতা।
ধরাকে সরা জ্ঞান করা আমরা সকলেই উপহাসের বিষয় মনে করি, কিন্তু সরাকে ধরা জ্ঞান করা আমাদের কাছে একটা মহৎ জিনিস। কারণ ও মনোভাবটি না থাকলে বিজ্ঞ হওয়া যায় না। বাক French Revolution -রূপ বিপুল রাজ্যবিপ্লবের সমালোচনাসত্রে যে মতামত ব্যক্ত করেছেন, সেই মতামত বালবিধবাকে জোর করে বিধবা রাখবার স্বপক্ষে, ও কৌলিন্যপ্রথা বজায় রাখবার স্বপক্ষে প্রয়োগ করলে যে আর-পাঁচজনের হাসি পাবে না কেন, তা বুঝতে পারি নে।
আমাদের সমাজ ও সামাজিক নিয়ম বহুকাল হতে চলে আসছে, আচারে ব্যবহারে আমরা অভ্যাসের দাস। আমাদের শিক্ষা নূতন, সে শিক্ষায় আমাদের মনের বদল হয়েছে। আমাদের সামাজিক ব্যবহারে ও আমাদের মনের ভাবে মিল নেই। যাঁরা মনকে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ বলে বিশ্বাস করেন, তাঁদের সহজেই ইচ্ছা হয় যে ব্যবহার মনের অনুরেপ করে আনি। অপরপক্ষে যাঁরা দুর্বল ভীরু ও অক্ষম অথচ বুদ্ধিমান, তাঁরা চেষ্টা করেন তর্কযুক্তির সাহায্যে মনকে ব্যবহারের অনুরূপ করে আনি। এই উদ্দেশ্যে যে তর্ক যুক্তি খুঁজেপেতে বার করা হয়, তারই নাম বিজ্ঞভাব। আমরা বাঙালিজাতি সহজেই দুর্বল ভীরু ও অক্ষম, সুতরাং স্বভাবের বলে আমরা না ভেবেচিন্তে বিজ্ঞের পদানত হই— এই হচ্ছে সার কথা।
বৈশাখ ১৩০৯