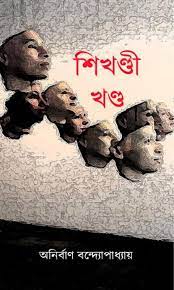- বইয়ের নামঃ শিখণ্ডী খণ্ড
- লেখকের নামঃ অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়
- প্রকাশনাঃ আরোহী
- বিভাগসমূহঃ গল্পের বই
শিখণ্ডী খণ্ড – অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়
উৎসর্গ : আমার পরম শুভানুধ্যায়ী পাঞ্চালী গুহকে
.
সূচিমুখ
- শিখণ্ডী খণ্ড
- অস্পৃশ্যনামা
- মৃত্যুদণ্ড : রাষ্ট্র কর্তৃক নরমেধ যজ্ঞ
.
মুখবন্ধ
‘শিখণ্ডী খণ্ড’ গ্রন্থটিতে তিনটি প্রমাণ আকারের প্রবন্ধ নিয়ে সংকলিত হয়েছে। এমন তিনটি বিষয় নিয়ে প্রবন্ধগুলো লেখা হয়েছে, মানুষের কৌতূহল সীমাহীন। মানুষের সেই কৌতূহলের পিপাসা মেটাতেই এই তিনটি প্রবন্ধ রচনার মূল উদ্দেশ্য। বিষয় তিনটি হল –শিখণ্ডী খণ্ড, অস্পৃশ্যনামা এবং মৃত্যুদণ্ড।
‘শিখণ্ডী খণ্ড’ প্রবন্ধের বিষয় এলজিবিটি (LGBT)। অর্থাৎ তথাকথিত হিজড়া, রূপান্তরকামী, সমকামী জন্ম, মৃত্যু, উৎসব, ধর্ম, জীবন, যৌবন ও যৌনতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা। হিন্দুসমাজে তথাকথিত হিজড়ারা ব্রাত্য, ঘৃণ্য, প্রান্তিক। তাঁদের সম্মানের চোখে দেখা হয় না। এঁদের নিয়ে খিল্লি করা যায়, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা যায়। এঁরা হাসির খোরাক। তাই এঁরা সমাজের মূল্যস্রোতকে এড়িয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে নিজস্ব কমিউনিটিতে। সমাজবিজ্ঞানী অ্যান ওকলের মতে, ‘জৈবিক লিঙ্গ’ শারীরিক বৈশিষ্ট্য বহন করে। আর ‘মানসিক লিঙ্গ’ একটি নির্দিষ্ট সমাজে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে নির্ধারিত বিশিষ্ট নির্দেশ করে। একজন নারী ও পুরুষের কার কী রকম পোশাক-পরিচ্ছদ হবে; কে কী রকম আচার-আচরণ করবে; আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা কার কী রকম হবে; সমাজের নানা ধরনের কাজে একজন নারী বা একজন পুরুষের ভূমিকা কী হবে এই বিষয়গুলো নির্ধারণ করে জেন্ডার বা লিঙ্গ। অর্থাৎ, ‘জৈবিক লিঙ্গ’ বিষয়টি পুরোপুরি শরীরের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু মানসিক লিঙ্গ নির্ভরশীল সমাজের উপর।
অনেকে মনে করেন সমকামিতা স্বাভাবিক ও সৃষ্টিশীল নয়, তাই ওরা সমাজের ব্রাত্য। যৌন-অভিমুখিতা নির্ধারণে যে সন্তানপালন বা শৈশবের অভিজ্ঞতার কোনো ভূমিকা আছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সমলিঙ্গের প্রতি যৌন আচরণের প্রভাবক হিসাবে এক পরিবেশে থাকার ভূমিকা মহিলাদের ক্ষেত্রে নগণ্য এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে শূন্য। কেউ কেউ সমকামী যৌনাচরণকে অপ্রাকৃতিক মনে করলেও বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে জানা গেছে সমকামিতা মানব যৌনতার একটি সাধারণ ও প্রাকৃতিক প্রকার মাত্র এবং অন্য কোনো প্রভাবকের অস্তিত্ব ছাড়া এটি মনের উপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলে না। অধিকাংশ মানুষের অভিজ্ঞতায় যৌনতার ব্যাপারে সচেতন পছন্দের কোনো ভূমিকা থাকে না। যৌন অভিমুখিতা পরিবর্তনের বিভিন্ন কর্মসূচির কার্যকারিতা সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ নেই। এরকম অনেক অজানা তথ্য উপস্থাপনার মধ্য দিয়েই এই প্রবন্ধ।
‘অস্পৃশ্যনামা’ প্রবন্ধে আলোচনা হয়েছে ভারতীয় নিম্নবর্গীয় গোষ্ঠী তথা শূদ্র তথা দলিতদের কথা। ব্রাহ্মণবাদীদের অত্যাচার ও ঘৃণা নিয়ে একটি গোষ্ঠীর ইতিহাস। নারদ ‘বিষ্ণুসংহিতা’ গ্রন্থে ব্রাহ্মণদের অবধ্য ও শারীরিক শাস্তিভোগের অতীত বলেছেন। গুপ্তযুগেই পুরোহিত শ্রেণি ভগবানের প্রতিনিধি হয়ে গেলেন। সেই কারণেই তাঁদের সাত খুন মাফ। সেইসঙ্গে রাজারাও যে ভগবানের প্রতিনিধি ও দৈবশক্তিসম্পন্ন, সেটাও প্রচার হতে থাকল। সেটা নথি হিসাবে মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে সংযোজিত হয়। বিষ্ণুসংহিতাতে বলা হয়েছে, “নিম্নশ্রেণির মানুষ উচ্চশ্রেণির মানুষের আসনে বসলে সেই নিম্নশ্রেণির নিতম্বে আগুনের ছাপ দিয়ে নির্বাসিত করে দেবে।” শূদ্রদের উদ্দেশ্যে আরও বলা হয়েছে –“সে যদি থুতু ফেলে তাঁর ঠোঁট কেটে দেবে।” বলা হয়েছে– “শূদ্র জাতিচ্যুত, তাই কোনো জাতিচ্যুত ব্যক্তি সাক্ষীরূপে গৃহীত হবে না।”
ঋগবেদের যুগেই যে চারটি বর্ণের উৎপত্তি হয়েছিল তার বীজ বা প্রমাণ পুরুষ সুক্ত (১০/৯০)। সেখানে দ্বাদশ ঋকে আছে পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ হল, দুই বাহু বা হাত থেকে রাজন্য হল, দুই ঊরু থেকে বৈশ্য হল এবং দুই চরণ বা পা থেকে শূদ্র হল— “লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহুরুপাদতঃ।/ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশং শূদ্রঞ্চনিরবর্তয়ৎ।।” মুসলিম শাসনের প্রায় ৮০০ বছরে এই ভারত উপমহাদেশে জাতপাত নিয়ে বহু জলঘোলা হয়েছে। জাতপাতের ঘৃণা থেকে মুক্তি পেতে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষগুলো বারবার অবস্থান পরিবর্তন করেছে। ধর্মান্তরিত হয়েছে। গোষ্ঠী বদল করেছে। জাতপাতের ইস্যু নিয়ে মুসলিম শাসন চলাকালীনই উত্থান হয়েছে ব্রাহ্মসমাজ, বৈষ্ণব আন্দোলন, খ্রিস্টান বা মিশনারিদের।
ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ঠিক যেভাবে হিন্দু নিম্নবর্গীয়দের ঘৃণ্য ও অচ্ছুৎ ভাবত, ঠিক সেই সূত্রেই মুসলিম হয়ে যাওয়া নিম্নবর্গীয়দের ঘৃণ্য ও অদ্যুৎ করল। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তথাপি নিম্নবর্গীয়দের যথাযথ সম্মান জানিয়ে ফিরিয়ে আনার ন্যূনতম চেষ্টা করেনি। সেদিন যদি ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ব্রাহ্মণ্যবাদে কিঞ্চিৎ শিথিলতা এনে নিম্নবর্গীয়দের যথাযোগ্য সম্মান না জানাতে পারত, তাহলে কখনোই এত সংখ্যক হিন্দু সম্প্রদায় থেকে মানুষ ইসলাম ও বৌদ্ধধর্মে কনভার্ট হয়ে যেত না।
একটা বিশাল জনগোষ্ঠীকে অস্পৃশ্য বলে কোণঠাসা করে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা কীভাবে সনাতন ধর্মের ক্ষতিসাধন করেছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।
তৃতীয় প্রবন্ধটির বিষয় হল মৃত্যুদণ্ড। চরমতম শাস্তি হিসাবে রাষ্ট্র একজন দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে থাকে। অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিকল্পিতভাবে হত্যা করে। মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমে রাষ্ট্র কর্তৃক নরমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করে। যেহেতু মানুষ নিজেকে তথা জীবন সৃষ্টি করে না, সেহেতু মানুষের কোনো অধিকার নেই কোনো মানুষের জীবন ধ্বংস করার। উপরন্তু কোনো ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তি (রাষ্ট্র) কোনো ক্ষমতা/অধিকার দেয়নি দোষীকে হত্যা করার। সাধারণ সময়ে শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ডের প্রয়োজনীয়তা নেই। কারণ এই শাস্তির কোনো প্রতিরোধক প্রভাব নেই সমাজে। মৃত্যুদণ্ড দর্শকদের মনে শুধুমাত্র ক্ষণিকের ছাপ ফেলে, তা স্থায়ী ছাপ ফেলতে পারে না।
তা ছাড়া judgment of Error হলে আর ফেরানো যাবে না মৃত্যুদণ্ডে ঝোলানো দণ্ডিতকে! সে কারণেই অপরাধ করলে কী কারণে অপরাধ করেছে, কোথায় ভুল ছিল এসব না ভেবে, ভুলগুলি শোধরানোর চেষ্টা না-করে অপরাধীকে জেলে ভরা হয়, অথবা হত্যা বা খুন করা হয়। আসলে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে অনেক সমস্যার চটজলদি সমাধান করতে চায় রাষ্ট্রগুলি। কিন্তু এতে সমস্যার সত্যিকারের সমাধান হয় না।
সাধারণত দেখা যায়, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা ও বিত্তশালীরা বিভিন্নভাবে মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যায়। কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠ ও গরিবরা মৃত্যুদণ্ডের শিকার হয়। মৃত্যুদণ্ড সহিংসতার কালচারকে উৎসাহিত করে। ফলে দেশে সহিংসতা বেড়ে যায়। মৃত্যুদণ্ড মানুষের মৌলিক অধিকার লংঘন করে। মৃত্যুদণ্ড যিনি দেন, মৃত্যুদণ্ড যিনি কার্যকর করেন, মৃত্যুদণ্ডের মতো হত্যাকাণ্ড যে বা যাঁরা সমর্থন করে উল্লসিত হন তাঁরা প্রত্যেকেই হত্যাকারী। হত্যার সপক্ষে যাঁরা বক্তৃতা দেন, আসলে তাঁদের অন্তরের ভিতর হত্যার স্পৃহা জেগে থাকে। নির্দোষ ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড হয়েছে এমন ঘটনা গোটা বিশ্বের সব দেশেই প্রভূত সংখ্যক হয়েছে। বর্ণবিদ্বেষ ও দারিদ্রতার কারণেও বহু নির্দোষের মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেছে। আর-একটি হল জনমতের চাপ, যা মিডিয়াগুলি লাগাতার তৈরি করে। চার্লি এল, ব্ল্যাকের গবেষণায় উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। সেখানে বলা হচ্ছে আমেরিকার ফৌজদারি ন্যায় ব্যবস্থাটাই শুধু ভুলপ্রবণই নয়, নেই কোনো নির্দিষ্ট মান। স্বেচ্ছাচারী ও চূড়ান্তভাবে শ্বেতাঙ্গ-ঘেঁষা এবং কৃষ্ণাঙ্গ-বিদ্বেষী। জর্জিয়াতে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গবেষণা করে অধ্যাপক ডেভিড বলডাস জানিয়েছেন –একজন শ্বেতাঙ্গকে হত্যা করা শ্বেতাঙ্গের মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার সম্ভাবনার চেয়ে কৃষ্ণাঙ্গ হত্যাকারী শ্বেতাঙ্গের মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার সম্ভাবনা ৮ গুণ কম। শ্বেতাঙ্গ হত্যাকারী কৃষ্ণাঙ্গের সেখানে মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার সম্ভাবনা ৩৩ গুণ বেশি। ভারতের মতো দরিদ্রতম দেশগুলিতে বর্ণ-বৈষম্য কোনো ম্যাটার না করলেও বিচার-বৈষম্য দেখা যায় দরিদ্রদের ক্ষেত্রে। ফৌজদারি মামলা সব ধরনের বৈষম্যের শিকার হয় দরিদ্ররাই– সে অভিযুক্তই হোক বা অভিযোগকারী। আইন আইনের পথে চললেও সেই আইনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত দরিদ্ররা। দারিদ্রতার কারণেই আইনের চোখে সবাই সমান হতে সক্ষম হয় না।
বিচারের একটি মানদণ্ডে মাদ্রাজ হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চ ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে আত্থাপ্পা গৌদমকে প্রাণদণ্ড দেয়। দরিদ্র হওয়ার কারণে সে তাঁর পরিবার প্রিভি কাউন্সিলে যেতে পারেননি আপিলের জন্য। তাঁর ফাঁসি কার্যকর হয়ে যায়। প্রায় ১০ বছর বাদে অন্য একটি সমধর্মীয় মামলায় প্রিভি কাউন্সিলে বিষয়টি বিশ্লেষিত হয় ও ফাঁসি দেওয়া ভুল হয়েছিল –একথা বলা হয়। গ্রেট ব্রিটেনে টিমোনি জন ইভান্সকে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে ফাঁসি দেওয়া হয়। পরে জানা যায় সে নির্দোষ ছিল। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে ইভান্সকে মরণোত্তর নির্দোষ ঘোষণা করা হয়। খুনের অভিযোগে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ডেরেক বেন্টলের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুলাই আদালত পুনর্বিবেচনা করে বলে বেন্টলের অপরাধী সাব্যস্ত হওয়াটা ছিল ‘unsafe’। নির্দোষ বেন্টলের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ঘটনা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।
পরিশেষে জানাই তিনটি প্রবন্ধের বিষয় এমনই যে দ্বিমত থাকতে পারে। দ্বিমত থাকাটাই স্বাভাবিক। তা ছাড়া কোনো বিষয়ে সকলেই যে আমার মতের সঙ্গে একমত হবেন এমন আশাও করি না। কার যুক্তি কুযুক্তি, কার যুক্তি সুযুক্তি, তা নির্ভর করে ব্যক্তির মননশীলতার উপর। অতএব আমার লেখা বিচার করার দায়িত্ব মননশীল পাঠকদের জন্যেই ছেড়ে রাখলাম। সবশেষে এটাই বলি, এই গ্রন্থটি পাঠ করে একজন পাঠকও সমৃদ্ধ ও ঋদ্ধ হয়, তবে আমি বলতেই পারি –আমার পরিশ্রম সার্থক।
শিখণ্ডী খণ্ড
“I want to suck your big penis”– চমকাবেন না। ফেসবুকের ইনবক্সে এরকম মেসেজ পাওয়ার এরকম নাছোড় অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই অনেকেরই হয়েছে। ফেসবুকে এরকম অনেক নারীপুরুষ তাঁদের যৌনসঙ্গী খুঁজতে সরাসরি এইভাবে প্রস্তাব রাখে। এরা আদতে সমকামী। পুরুষ খোঁজে পুরুষকে, নারী খোঁজে নারীকে। প্রথমপক্ষ ‘গে’, অপরপক্ষ ‘লেসবিয়ান’। বাজারি নাম ‘হিজড়ে’ বা ‘হিজড়া’ রূপান্তরকামী বা ট্রান্সসেক্সয়ালও বলা হয়ে থাকে। সোজা বাংলায় যৌনপ্রতিবন্ধী বা লিঙ্গ-কবন্ধ জাতক বলা যায়।
হিজড়া দক্ষিণ এশিয়ায় ব্যবহৃত একটি পরিভাষা— বিশেষ করে ভারতের ট্রান্সসেক্সয়াল বা ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিকে বুঝিয়ে থাকে।চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় ক্রোমোজোমের ত্রুটির কারণে জন্মগত যৌনপ্রতিবন্ধী ব্যক্তি, যাদের জন্ম-পরবর্তী লিঙ্গ নির্ধারণে জটিলতা দেখা দেয়, মূলত তাঁরাই হিজড়া। হিজড়া শব্দের অপর অর্থ হচ্ছে ‘ট্রান্সজেন্ডার’, ট্রান্সজেন্ডার বলতে এমন এক লৈঙ্গিক অবস্থাকে বোঝায় যা দৈহিক বা জেনেটিক কারণে মেয়ে বা ছেলে কোনো শ্রেণিতে পড়ে না। প্রকৃতিতে কিছু মানুষ নারী এবং পুরুষের যৌথ বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। বাংলা ভাষায় এই ধরনের মানুষগুলো হিজড়া নামে পরিচিত। সমার্থক শব্দে শিখণ্ডী, বৃহন্নলা, তৃতীয় লিঙ্গ, উভলিঙ্গ, নপুংসক, ট্রান্সজেন্ডার (ইংরেজি), ইনুখ (হিব্রু), মুখান্নাতুন (আরবি), মাসি, বৌদি, চাচা, তাউ, ওস্তাদ, মাংলিমুখী, কুলিমাদর, ভিলাইমাদর, মামা, পিসি, অজনিকা ষণ্ড, অজনক, সুবিদ, কঞ্চুকী, মহল্লক, ছিন্নমুষ্ক, আক্তা, পুংস্তহীন ইত্যাদি। হরিদ্বারে হিজড়াদের সকলে তাওজি বা পণ্ডিতজি বলে পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মে হিজড়াদের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
হিজড়া, সমকামী, উভকামী, রূপান্তরকামী– এঁরা না-নারী না-পুরুষদের দলে অন্তর্ভুক্ত হলে এঁদের সূক্ষ্ম মূলগত পার্থক্য আছে। সবাইকে পাইকারি দরে এক পংক্তিতে ফেলা যাবে না। প্রথমে আসি হিজড়া প্রসঙ্গে।
হিজড়া : লিঙ্গ ও অণ্ডকোশ কর্তন করে যাঁরা বাচ্চা নিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে তাঁরা হিজড়া বলে পরিচিত। বা যাঁরা প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও অপরিণত বা ত্রুটিপূর্ণ যৌনাঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তাঁদেরও হিজড়া বলা হয়। এঁরা সমকামী হতে পারে আবার নাও হতে পারে। এঁরা সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।
সমকামী : সমকামিতা (Homosexuality) বলতে বোঝায় সমলিঙ্গ ব্যক্তির প্রতি আকর্ষণ ও দুর্বলতা বোধ করে। যৌনতা করতে মন চায়। অর্থাৎ যাবতীয় রোম্যান্টিক আকর্ষণ, যৌন আকর্ষণ ও যৌন আচরণকে বোঝায়। যৌন অভিমুখিতা হিসাবে। সমলিঙ্গ বলতে শারীরিকভাবে পুরুষ শরীরের অধিকারী হয়েও পুরুষ শরীরের প্রতি যৌন আকর্ষণ এবং শারীরিকভাবে নারী শরীরের অধিকারী হয়েও নারী শরীরের প্রতি যৌন আকর্ষণ বোঝায়। এঁরা সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।
উভকামী : এঁরাও সমকামী। তবে এঁরা বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তিদের সঙ্গে যৌনানন্দ উপভোগ করে। এঁরা বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তিদের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেও সমলিঙ্গের বন্ধু খুঁজে নিয়ে তাঁর সঙ্গে যৌন সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে যায়। এঁরা সমাজের মূলস্রোতেই থাকে।
রূপান্তরকামী : রূপান্তরকামিতা (Transsexualism) বলতে বিশেষ একটি প্রবণতা বোঝায় যখন জৈব লিঙ্গ ব্যক্তির জেন্ডারের সঙ্গে প্রভেদ তৈরি করে। রূপান্তরকামী ব্যক্তিরা এমন একটি যৌন পরিচয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করেন, যা ঐতিহ্যগতভাবে তাঁদের নির্ধারিত যৌনতার সঙ্গে স্থিতিশীল নয় এবং | নিজেদেরকে স্থায়ীভাবে সেই লিঙ্গে পরিবর্তন করতে চান। রূপান্তরকামী। মানুষেরা পুরুষ হয়ে (বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে) জন্মানো সত্ত্বেও মন-মানসিকতায় নিজেকে নারী ভাবেন এবং নারী হিসাবে জন্মানোর পরও মানসিক জগতে থাকেন পুরুষসুলভ। এঁদের কেউ কেউ বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরিধান করেন, এই ব্যাপারটিকে বলা হয় ট্রান্সভেস্টিজম বা ক্রসড্রেস। আবার কেউ সেক্স রিঅ্যাসাইনমেন্ট সার্জারির মাধ্যমে রূপান্তরিত মানবে (Transexual) পরিণত হন। যেমন সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে মানবী বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে যাওয়া। এঁরা সকলেই রূপান্তরিত লিঙ্গ নামক বৃহৎ রূপান্তরপ্রবণ সম্প্রদায়ের (Transgender) অংশ হিসেবে বিবেচিত।
মানবসভ্যতার বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় লিখিত ইতিহাসের সমগ্র সময়কাল জুড়ে রূপান্তরকামিতার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে আমেরিকার পুরুষ রূপান্তরকামী জর্জ জরগেন্সেনের ক্রিস্টিন জরগেন্সেনের রূপান্তরিত হওয়ার কাহিনি মিডিয়ায় একসময় আলোড়ন তুলেছিলো। এ ছাড়া জোয়ান অব আর্ক, জীববিজ্ঞানী জোয়ান (জনাথন) রাফগার্ডেন, বাস্কেটবল খেলোয়াড় ডেনিস রডম্যান, চক্ষুচিকিৎসক এবং পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় ডঃ রেনি রিচার্ডস, সঙ্গিতজ্ঞ বিলিটিপটন সহ অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির মধ্যে রূপান্তর প্রবণতার উল্লেখযোগ্য ইতিহাসে পাওয়া যায়। ১৯৬০ সালে মনোচিকিৎসক ওয়ালিন্দার রূপান্তরকামীদের উপরে একটি সমীক্ষা চালান। তাঁর এই সমীক্ষা থেকে জানা যায়, প্রতি ৩৭,০০০ জনের মধ্যে একজন পুরুষ রূপান্তরকামীর জন্ম হচ্ছে, অন্যদিকে প্রতি ১০৩,০০০ জনের মধ্যে একজন স্ত্রী রূপান্তরকামীর জন্ম হচ্ছে। ইংল্যান্ডে এই সমীক্ষাটি চালিয়ে দেখা গেছে যে, সেখানে প্রতি ৩৪,০০০ জনের মধ্যে একজন পুরুষ রূপান্তরকামী ভূমিষ্ট হচ্ছে, আর অন্যদিকে প্রতি ১০৮,০০০ জনের মধ্যে একজন জন্ম নিচ্ছে একজন স্ত্রী রূপান্তরকামী। অস্ট্রেলিয়া আর নিউজিল্যান্ডে গবেষণা চালিয়ে দেখা গেছে, সেখানে ২৪,০০০ পুরুষের মধ্যে একজন এবং ১৫০,০০০ নারীর মধ্যে একজন রূপান্তরকামীর জন্ম হয়। এ বিষয়ে আরও পরে বিস্তারিত লিখব।
ধর্মবেত্তারা হিজড়াদের নিয়ে বিপুল শ্রম খরচ করে ভয়ানক ভ্রম সৃষ্টি করে রেখেছেন। ঘৃণা আর অবজ্ঞা ছড়িয়ে রেখেছেন। তা সত্ত্বেও হিজড়ারা কেউ নাস্তিক নয়। তথাকথিত ‘ঈশ্বরের এই বিধান ও ধর্মীয় অনুশাসনকে মাথায় পেতে নিয়ে নিজেদেরকে ‘অভিশপ্ত’ বলেই গোটা জীবন কাটিয়ে দেন। আসুন দেখি, ধর্মগ্রন্থগুলি কী বলছে জেনে নেওয়া যাক।
.
ইসলাম ধর্মে হিজড়া
হজরত ইব্রাহিমের বংশধরদের মাধ্যমে পৃথিবীর বুকে প্রচারিত ধর্মগুলোকে একসঙ্গে বলা হয় ইব্রাহিমীয় ধর্ম ইসলাম, খ্রিস্টধর্ম, ইহুদি ধর্ম— এগুলো সবই ইব্রাহিমীয় ধর্ম। প্রতিটি ইব্রাহিমীয় ধর্ম পুরুষ এবং নারী সৃষ্টির ব্যাপারে আদম এবং হাওয়া (ইভ)-এর গল্প বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ প্রথমে মাটি থেকে তৈরি করেন আদমকে। আদমের বুকের পাঁজর দিয়ে তৈরি করেন বিবি হাওয়াকে। তাহলে আল্লাহ তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ কিভাবে তৈরি করেন? নারী ও পুরুষের পাশাপাশি তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ বা হিজড়া কীভাবে সৃষ্টি করা হল, এই বিষয়ে পৃথিবীর কোনো ধর্মেই আলোচনা করা হয়নি।
ইসলামে তৃতীয় লিঙ্গ বা হিজড়াদের মুখান্নাতুন হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আরবি ভাষায় ‘মুখান্নাতুন’ বলতে মেয়েদের মত আচরণকারী পুরুষদেরকে বোঝানো হয়। এক্ষেত্রে যেহেতু শুধুমাত্র মেল টু ফিমেল ট্রান্সসেক্সয়ালদের বোঝানো হয়, তাই আরবি ‘মুখান্নাতুন’ হিব্রু সারিস বা ইংরেজি ‘ইউনুখ’-এর সমার্থক শব্দ নয়। কোরানে কোথাও মুখান্নাতুন সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। কিন্তু হাদিসে ‘মুখান্নাতুন’-এর উল্লেখ পাওয়া যায়।
নবি বর্ণিত হাদিস থেকে জানা যায়, একজন মুখান্নাতুন’ হচ্ছে সেই পুরুষ, যাঁর চলাফেরায়, চেহারায় এবং কথাবার্তায় নারী আচরণ বহন করে। তাঁরা দু-প্রকারের— প্রথম প্রকারের হচ্ছে তাঁরাই যাঁরা এই ধরনের আচরণ ইচ্ছাকৃতভাবে করে না এবং তাঁদের এই ব্যবহারে কোনো দোষ নেই, কোনো অভিযোগ নেই, কোনো লজ্জা নেই যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা কোনো অবৈধ কাজ না করে এবং গণিকাবৃত্তিতে না জড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় শ্রেণির ব্যক্তি হচ্ছে তাঁরাই যাঁরা অনৈতিক উদ্দেশ্যে মেয়েলি আচরণ করে।
হজরত ইবনে আব্বাস বলেছেন– হিজড়ারা জিনদের সন্তান। এক ব্যক্তি আব্বাসকে প্রশ্ন করেছিলেন– এটা কেমন করে হতে পারে? জবাবে তিনি বলেছিলেন– “আল্লাহ ও রসুল নিযেধ করেছেন যে মানুষ যেন তাঁর স্ত্রীর পিরিয়ড বা মাসিক স্রাব চলাকালে যৌনমিলন না করে”। সুতরাং কোনো মহিলার সঙ্গে তাঁর ঋতুস্রাব হলে শয়তান তাঁর আগে থাকে এবং সেই শয়তান দ্বারা ওই মহিলা গর্ভবতী হয় এবং হিজড়া সন্তান (খুন্নাস) প্রসব করে (সুরা বাণী ইস্রাইল –আর রাহমান-৫৪, ইবনে আবি হাতিম, হাকিম তিরমিজি)।
“তিনিই মহান সত্ত্বা, মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছে তোমাদের আকৃতি গঠন করেন। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।” (সুরা আলে ইমরান ৬) ইসলামীদের মতে তিনি মানবজাতির কারোকে পুরুষ, কারোকে নারী, আবার তাঁর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ স্বরূপ কারোকে বানিয়েছেন একটু ভিন্ন করে। যেন বান্দা তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতা সম্পর্কে জানতে পারে যে তিনি সব বিষয়ে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যেমন স্বাভাবিক সুন্দর সৃষ্টি করতে সক্ষম, তেমনি এর ব্যতিক্রম সৃষ্টি করতেও সক্ষম। আর এমনই এক বৈচিত্র্যময় সৃষ্টি হল লিঙ্গ প্রতিবন্ধী বা হিজড়া। এঁরা পূর্ণাঙ্গদের মতো সমান মর্যাদার অধিকারী মানবগোষ্ঠী।
ইসলামের দৃষ্টিতে হিজড়া, বিকলাঙ্গ বা পূর্ণাঙ্গ হওয়া মর্যাদা-অমর্যাদার মাপকাঠি নয়। বরং তাকওয়াই হল মানমর্যাদা আর শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি। “আল্লাহতাআলা তোমাদের বাহ্যিক আকার-প্রকৃতি এবং সহায়-সম্পত্তির প্রতি লক্ষ করেন না। বরং তিনি লক্ষ করেন তোমাদের অন্তর এবং আমলের প্রতি।” (সহিহ মুসলিম, হাদিস নম্বর ৬৭০৮) অতএব ইসলামি মূল্যবোধ ও সুমহান আদর্শের আলোকে এটাই প্রমাণিত হয়, লিঙ্গ প্রতিবন্ধীদের এ পরিমাণ সম্মান ও মর্যাদা আছে, যে পরিমাণ মর্যাদা ও সম্মান আছেএকজন সুস্থ-সবল সাধারণ মুসলিমের। এমনকি ইসলামি শরিয়তে একজন মুমিন-মুত্তাকি, পরহেজগার হিজড়া, শত-সহস্র কাফের-ফাসেক ও মুত্তাকি নয় এমন নরনারী থেকে উত্তম। শরিয়তের পরিভাষায় তাঁকেই হিজড়া বলা হয়, যাঁর পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ উভয়ই আছে। অথবা কোনোটিই নেই, শুধু মূত্রত্যাগের জন্য একটিমাত্র ছিদ্রপথ আছে। সংক্ষেপে একই শরীরে স্ত্রী ও পুরুষচিহ্ন যুক্ত অথবা উভয় চিহ্নবিযুক্ত মানুষই হল লিঙ্গ প্রতিবন্ধী বা হিজড়া (কামুসুল ফিকহ ৩/৩৭৭)। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা মনে করেন, কোনো পুরুষ বা নারী নিজ ইচ্ছায় নারী ও পুরুষ হয়নি। তেমনি হিজড়া হওয়ার পিছনেও তাঁদের নিজের ইচ্ছার কোনো ভূমিকা নেই। এটা শুধুমাত্র আল্লাহতালার কুদরতের বহিঃপ্রকাশ। তিনি নিজের ইচ্ছায় বানিয়েছেন উভলিঙ্গ বা হিজড়া। কোরানের আলোকে বোঝা যায়, এর পিছনে আল্লাহর মহান হেকমত ও নিগূঢ় রহস্য বিরাজমান। ইসলামী দেশগুলির মধ্যে ইরানে সবচেয়ে বেশি রুপান্তরকামী অপারেশন করা হয়। তারা তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিকে যে-কোনো এক লিঙ্গে রুপান্তর হওয়ার সুযোগ দেয়।
.
হিন্দু ধর্মে হিজড়া
দক্ষিণ এশিয়ায় তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদেরকে সাধারণত হিজড়া নামে অভিহিত করা হয়। কিন্তু অঞ্চলভেদে ভাষাভেদে হিজড়াকে বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। এই অঞ্চলে হিজড়াদেরকে সামাজিক ভাবে মূল্যায়িত করা হয়। তারা সমাজ থেকে দূরে বাস করতে বাধ্য হয়। দূরপাল্লা ট্রেনে বা বাজারে ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তিই তাদের প্রধান পেশা।
হিন্দুদর্শনে তৃতীয় লিঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। নারী পুরুষের বৈশিষ্ট্য সম্বলিত এই শ্রেণিকে ‘তৃতীয় প্রকৃতি’ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে এই ধরনের মানুষকে আলাদাভাবে পুরুষ বা নারী হিসাবে বিবেচনা করা হত না। তাদেরকে জন্মসূত্রে তৃতীয় প্রকৃতি হিসেবে গণ্য করা হত। তাদের কাছে সাধারণ নারী-পুরুষের মতো ব্যবহার প্রত্যাশা করা হত না। আরাবানী হিজড়ারা আরাবান দেবতার পুজো করে। অনেক মন্দিরে হিজড়াদের নাচের ব্যবস্থা করা হয়। অনেক হিন্দু বিশ্বাস করেন হিজড়াদের আশীর্বাদ করার এবং অভিশাপ দেওয়ার বিশেষ ক্ষমতা আছে।
হিন্দু সংস্কৃতিতে এই মুহূর্তে তিনজন মহাকাব্যিক চরিত্রের কথা মনে পড়ছে– চিত্রাঙ্গদা, বৃহন্নলা এবং শিখণ্ডী। এঁরা হিজড়া বলেই পরিচিত হয়েছে, যদিও এঁরা কেউই সেই অর্থে হিজড়া নয়। এঁদের কারোরই যৌনাঙ্গের ত্রুটি ছিল না। তবু কেন চিত্রাঙ্গদা, বৃহন্নলা এবং শিখণ্ডীরা ‘হিজড়া’ শব্দের সমর্থক হয়ে উঠল?
চিত্রাঙ্গদা মহাভারত মহাকাব্যের একটি চরিত্র। মণিপুরের রাজকন্যা চিত্রাঙ্গদা। মণিপুররাজের ভক্তিতে তুষ্ট হয়ে শিব বর দিয়েছিলেন যে তাঁর বংশে কেবল পুত্রই জন্মাবে। তা সত্ত্বেও রাজকুলে যখন চিত্রাঙ্গদা নামে কন্যার জন্ম হল, রাজা তাঁকে পুত্ররূপেই পালন করলেন। সেই সূত্রেই রাজকন্যা পুত্রের বেশে ধনুর্বিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা এবং রাজদণ্ডনীতি অনুশীলন করতে থাকলেন। মণিপুররাজ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, তাঁর কন্যার সঙ্গে কেবলমাত্র মহাবীর অর্জুনের বিবাহ দেবেন। অন্যদিকে ইন্দ্রপ্রস্থে অর্জুন মিলনরত অবস্থায় যুধিষ্ঠির ও দ্রৌপদীকে দেখে ফেললে তাঁর দ্বাদশ বর্ষ বনবাস হয়। অর্জুন দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী ব্রহ্মচর্য ব্রত পালনের সময় ভ্রমণ করতে করতে মণিপুর রাজ্যে। সেই সময়ে অর্জুন চিত্রাঙ্গদার প্রেমে পড়েন। চিত্রাঙ্গদাকে বিবাহ করলেন। তাঁদের মিলনের ফলে অর্জুনের ঔরসে চিত্রাঙ্গদার গর্ভে সন্তান আসে। তাঁদের মিলনজাত পুত্রের নাম বজ্ৰবাহন। কিন্তু চিত্রাঙ্গদার মধ্য ক্রমশ দ্বৈতসত্ত্বার দ্বন্দ্ব শুরু হয় এজন্যে যে, অর্জুন তাঁকে বাহ্যিক রূপের কারণে ভালোবাসে সেখানে চিত্রাঙ্গদার প্রকৃত অস্তিত্ব অবহেলিত। এর মধ্যে মণিপুর রাজ্যের বিপদের আভাসে একসময় অর্জুন নারীর মমতায় প্রজাবৎসল, সাহসে-শক্তিতে পুরুষের মতো সবল চিত্রাঙ্গদার কথা লোকমুখে জানতে পারে। রবিঠাকুরের ভাষায় –
“শুনি স্নেহে সে নারী বীর্যে সে পুরুষ,
শুনি সিংহাসনা যেন সে সিংহবাহিনী।”
একজন পুরুষ-মনে একজন রমণীয় সবল নারীকে দেখার উদগ্র বাসনা অর্জুন প্রকাশ করে তাঁর আগ্রহ—
“আগ্রহ মোর অধীর অতি —
কোথা সে রমণী বীর্যবতী,
কোষবিমুক্ত কৃপাণলতা–
দারুণ সে, সুন্দর সে
উদ্যত বজ্রের রুদ্ররসে,
নহে সে ভোগীর লোচনলোভা,
ক্ষত্রিয়বাহুর ভীষণ শোভা।”
এমতাবস্থায় চিত্রাঙ্গদা নিজেকে অর্জুনের কাছে প্রকাশ করে এভাবে—
“আমি চিত্রাঙ্গদা, আমি রাজেন্দ্ৰনন্দিনী
নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।
পূজা করি মোরে রাখিবে ঊর্ধ্বে
সে নহি নহি,
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে
সে নহি নহি।
যদি পার্শ্বে রাখ মোরে
সংকটে সম্পদে,
সম্মতি দাও যদি কঠিত ব্ৰতে
সহায় হতে,
পাবে তবে তুমি চিনিতে মোরে।
পরিশেষে এটা উপলব্ধি হয় যে, বাহ্যিক রূপের চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান মানুষের চারিত্রিক শক্তি এবং এতেই প্রকৃতপক্ষে আত্মার স্থায়ী পরিচয়।
অতএব চিত্রাঙ্গদা যৌনত্রুটি ঘটিত হিজড়া বা রূপান্তরকামী ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি পূর্ণাঙ্গ নারী এবং নিজেকে নারী হিসাবেই পরিচয় দিতেন। নারী হয়েও পুরুষের পোশাক পরতেন ঠিকই এবং পুরুষদের মতো শিক্ষাগ্রহণও করেছিলেন। সেটা করেছিলেন পিতার ইচ্ছাপূরণ করতে। তাঁর শারীরিক প্রতিবন্ধকতা যেমন ছিল না, তেমন মানসিক বৈকল্যও ছিল না। কেন যে ‘চিত্রাঙ্গদা’ চলচ্চিত্রের পরিচালক ও অভিনেতা (অভিনেত্রী?) ঋতুপর্ণ ঘোষ বলেন –“পৌরুষের বদলে রূপলাবণ্য পাওয়ার বাসনাই ঘুরপাক খেয়েছে এই চলচ্চিত্রে।” চিত্রাঙ্গদার ভিতর লৈঙ্গিক বিষয়টা যে অনেক বড়ো আছে, তা নাকি আগে বুঝতে পারেননি ঋতুপর্ণ। চলচ্চিত্র যদি ভাষার মতো হবে, তাহলে সেই ভাষার পথ ধরে ঋতুপর্ণের অবচেতনের ঘরে কে বসত করত, তা সহজেই অনুমেয়। সেই বসতকারী পৌরুষ বিসর্জন দেওয়ার জন্য উদগ্রীব, নারীসুলভ লাবণ্য ঋতুপর্ণের কাম্য। চিত্রাঙ্গদায় ঋতুপর্ণ দেখিয়েছেন, শুদ্ধ বললে ভুল হবে, কারণ তিনি অভিনয়ও করেছেন এক রক্ষণশীল, বিত্তবান পরিবারের নারীসুলভ ছেলের চরিত্রে। যাঁকে প্রায় বাধ্য করা হয় পুরুষ হয়ে উঠতে। প্রসঙ্গত জানিয়ে রাখি ঋতুপর্ণ ঘোষ নিজেই রূপান্তকামী ব্যক্তিত্ব ছিল। তিনি পুরুষ হয়েও মেয়েদের পোশাক পরতেন, মেয়েদের মতো রূপচর্চাও করতেন। অবশেষে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে রূপান্তর হতে গিয়েই নাকি তাঁর অকালমৃত্যু হয়। প্রকৃত ঘটনা হল ১০ বছর ধরে উনি ডায়াবেটিস (ডায়াবেটিস মেটিলাস, টাইপ ২) অসুখে ভুগছিলেন। ৫ বছর ধরে প্যানক্রিটিটিস অসুখে ভুগছিলেন। এছাড়াও তাঁর অনিদ্রার সমস্যা ছিল। ফলে তিনি নিয়মিত ঘুমের ওষুধ খেতেন। চিকিৎসকদের রিপোর্ট অনুযায়ী, অ্যাবডোমিনোপ্ল্যাস্টি ও ব্রেস্ট ইমপ্ল্যান্টের পর প্রয়োজনীয় হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি করাতে গিয়ে তাঁর শারীরিক অসুস্থতা বেড়ে যায়। আরেকটি প্রেমের গল্প’ চলচ্চিত্রে এক সমকামী চিত্রপরিচালকের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য তাঁকে এগুলি করাতে হয়েছিল বলে শোনা যায়।
বৃহন্নলা > বৃহৎ + নল + আ। এর অর্থ দীর্ঘ ভুজা বা দীর্ঘ হাত। মহাভারতে অর্জুন অজ্ঞাতবাসের এক বছর নারীরূপে বিচরণ করেছিলেন। তিনি এসময় নিজের প্রকৃত নাম পরিবর্তন করে ‘বৃহন্নলা’ রাখেন। অর্জুনের দীর্ঘ হাত ছিল বলেই এরূপ নামকরণ অর্জুন যেহেতু স্বনামধন্য যোদ্ধার প্রকৃতির ছিলেন, তাই তিনি অন্য কোনো রূপ ধারণ না করে ‘নারী’ রূপ ধারণ করেন। মহাভারতের অর্জুন অজ্ঞাতবাসের প্রয়োজনে বলেছিলেন– আমি তৃতীয়া প্রকৃতির মধ্যে নিজেকে অন্তরীণ করে রাখব– “তৃতীয়াং প্রকৃতিং গতঃ”। অতএব বৃহন্নলা নামধারী অর্জুনও যৌনত্রুটিগত ‘হিজড়া’ ছিলেন না। শারীরিক ও মানসিকভাবেও সম্পূর্ণ সুস্থ ছিলেন। অর্জুন ছিলেন পূর্ণাঙ্গ পুরুষ, নারী-মনের পুরুষ নয়। সাময়িক কার্যসিদ্ধির জন্য অর্জুন নারীর পোশাক পরে নারীর মতো আচরণ করেছিলেন মাত্র। অতএব বৃহন্নলা কখনোই হিজড়ার সমর্থক হতে পারে না। কোনো পুরুষ কোনো কারণে নারীর সাজপোশাক পরলেই রূপান্তরকামী বলা যায় না। অথবা নারী পুরুষের পোশাক পরলেই রূপান্তরকামী বলা যায় না। মহাভারতের চিত্রাঙ্গদা ও বৃহন্নলা এক ধরনের চরিত্র।
একটা সময় ছিল যখন চলচ্চিত্র, নাটক, যাত্রায় নারীরা সামাজিক অন্তরায় থাকার জন্য অভিনয় করতে আসত না। সে সময় নারীচরিত্রে নারীর পোষাকে পুরুষরা অভিনয় করত। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফি, অমৃতলালবসুর মতো নটরাও প্রয়োজনে নারীচরিত্রে অভিনয় করত। সেই ধারার শেষের দিককার অন্যতম প্রতিনিধি চপল ভাদুড়ী। অভিনয়ের মঞ্চে নারীরা আসতে শুরু করেন ষাটের দশকের শেষের দিকে। তার আগে পর্যন্ত নারীচরিত্রে অভিনয় পুরুষ অভিনেত্রীরাই। অভিনেত্রী’ চপল ভাদুড়ী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। চপলবাবুর পারিশ্রমিকও ছিল বেশ চড়া।
স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে চপলবাবু বলেন— “১৫ বছর বয়স থেকে নারীচরিত্রে অভিনয় করছি। স্বাভাবিকভাবেই আমার মধ্যে অনেক নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য চলে এসেছে। কিন্তু আমি নারীসজ্জা নিয়েছি কেবল মঞ্চে। ঋতুর মতো জনসমক্ষে শাড়ি-গয়না পরে বের হইনি কখনো।” চপল ভাদুড়ী বায়োলজিক্যাল রূপান্তরকামী ছিলেন না। তা সত্ত্বেও তিনি সমকামী অপবাদে অপমানিত হয়েছেন। তাঁর ভাষায় –“সমকামিতার ‘অপরাধে’ দল থেকে বের করে দেওয়া হয়। বঞ্চিত করা হয় প্রাপ্য পারিশ্রমিক থেকেও। আমি অবাক হইনি, সেসময় সমলিঙ্গের মানুষের মধ্যে সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে বলা দূরে থাক, ভাবতও না লোকে।”
সারা পৃথিবী জুড়েই বহুকাল থেকে নারীচরিত্রের ভূমিকায় পুরুষ এবং পুরুষচরিত্রের ভূমিকায় নারীর অভিনয় করার দৃষ্টান্ত আছে। ডাস্টিন হফম্যান ‘টুটসি’ ও রবিন উইলিয়াম ‘মিসেস ডাউটফায়ার’ চলচ্চিত্রে যে চরিত্র করেছেন সেটা তেমনই। কিছু সময়ের জন্য নারী সেজেছেন মাত্র। গল্পের প্রয়োজনেই পুরুষ সেখানে কিছুক্ষণের জন্য নারীর ছদ্মবেশ নিয়েছে। এইরকম ভাবেই “মিসেস ডাউটফায়ার’ অবলম্বনে কমল হাসান করেছিল ‘চাচি ৪২০’। আমির খান, গোবিন্দা ও রীতেশ দেশমুখও এই মুভিতে নারীর ছদ্মবেশ নিয়েছিল। ঠিক যেভাবে ‘মিস প্রিয়ংবদা’ চলচ্চিত্রে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ঠিক সেভাবেই মহাভারতের অর্জুন বৃহন্নলা।
ওয়ালেস বিরি, ফ্যাটি আরবাকল, অ্যালেক গিনেস প্রমুখ অনেকেই নারীচরিত্রে দাপুটের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। পরের দিকে জেরি লিউইস, এডি মারফি, টেরি জোন্সের মতো অনেককে নারীচরিত্রে দেখা গেছে। হেয়ার স্পে’ চলচ্চিত্রে নারীচরিত্র করেই ‘গোল্ডেন গ্লোব’ জিতে নেন অভিনেতা জন ট্রাভোল্টা। হাবিব তনবিরের নির্দেশনায় ‘জিস লাহৌর নহি দেখা ওহ জামিয়া নেহি’ নাটকে নারীচরিত্রে পুরুষের অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়েছেন দর্শকরা।
ডাক্তার মাসুর গুলাটি। আসল নাম সুনীল গ্রোভারের তুলনায় এই নামেই বেশি জনপ্রিয় এই অভিনেতা। কপিল শর্মার অনুষ্ঠানে দীর্ঘদিন ধরে নারীচরিত্রে কমেডিয়ান হিসাবে তাঁর পরিচিতি। জনপ্রিয়তা তুঙ্গে হলেও তাঁর পুরুষসত্ত্বায় কখনো কি আঘাত এনেছে এই চরিত্র? এমন প্রশ্নের উত্তরে তাঁর সাফ কথা– বায়োলজিক্যাল পুরুষ হলেও নারী হতে তাঁর মন্দ লাগে না একফোঁটাও। সুনীল গ্রোভার রূপান্তরকামী নন, উনি একজন পূর্ণাঙ্গ পুরুষ।
ইরানে মেয়েরা ছেলে সেজে স্টেডিয়ামে খেলা দেখেছেন। প্রিয় দলের খেলা দেখতে পুরুষের সাজে স্টেডিয়ামে এসেছিলেন এসব নারীরা। ইরানের স্টেডিয়ামে নারীদের ঢুকতে দেওয়া হয় না। অবিকল ছেলেদের সাজ-পোশাক নিয়ে খেলা দেখেছেন। দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর এই ম্যাচে পেরেসপোলিসের বেশ কিছু নারী সমর্থক নকল দাড়ি আর পরচুলা পরে স্টেডিয়ামে ঢোকেন। নকল এই সাজ-পোশাক এতটাই নিখুঁত ছিল যে, স্টেডিয়ামের নিরাপত্তারক্ষীরা পর্যন্ত ধরতে পারেনি। এই নারীদের রূপান্তরকামী বলা যায় না। উদ্দেশ্য পৃথক হলেও বৃহন্নলা ও চিত্রাঙ্গদাকেও তেমনি রূপান্তরকামী বলা যায় না। তথাকথিত ‘হিজড়া’র প্রতিশব্দও হতে পারে না।
শিখণ্ডী মহাভারতের আর-একটি চরিত্র। দ্রুপদের মেয়ে ও দ্রৌপদীর বড়ো বোন! কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁর পিতা দ্রুপদ ও ভাই ধৃষ্টদুম্নের সঙ্গে পাণ্ডবদের পক্ষে যুদ্ধ করেছিলেন। এবং ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ হয়েছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম ক্ষত্রদেব। পূর্বজন্মে শিখণ্ডী ছিলেন কাশীরাজের বড়ো মেয়ে অম্বা। হস্তিনাপুরে রাজা বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য ভীষ্ম তাঁর দুই বোন সহ তাঁকে স্বয়ংবর সভা থেকে জয় করে নিয়ে যান। কিন্তু তিনি সুবলের রাজা শান্বকে ভালোবাসেন জেনে বিচিত্রবীর্য তাঁকে বিয়ে করেননি। শাল্বও পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে তাঁকে বিয়ে করতে রাজি না হওয়ায় তাঁর দুর্দশার জন্য তিনি ভীষ্মকে দায়ী করেন এবং ভীষ্মের মৃত্যু কামনায় সাধনা করে শিবের বর লাভ করে ‘শিখণ্ডী’ নামে দ্রুপদ রাজার মেয়ে হিসাবে জন্মগ্রহণ করেন।
শৈশবে শিখণ্ডী রাজপ্রাসাদের ফটকে রাখা একটা মালা গলায় পরে দ্রুপদের কাছে এলে দ্রুপদ বুঝতে পারেন, শিখণ্ডীই অম্বা। কারণ কার্তিকের প্রদত্ত চিরসবুজ পদ্মের মালাটি শুধু অম্বাই পরতে পারে। তখন রাজা ভীষ্মের আক্রমণ এড়ানোর জন্য শিখণ্ডীকে বনে রাখার ব্যবস্থা করেন। সেখানে শিখণ্ডী সাধনা করে স্থণাকর্ণ নামে এক যক্ষের কাছ থেকে পুরুষত্ব লাভ করে। মহাভারতের যুগে সফল ট্রান্সজেন্ডার! অথচ একবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় সোমনাথ থেকে মানবী হতে কত কসরৎই-না করতে হল। যাই হোক, এরপর শিখণ্ডী বন থেকে রাজপ্রাসাদে ফিরে আসে এবং বিয়ে করে সংসারী হন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পুরুষ-যোদ্ধা হিসাবেই অংশগ্রহণ করেছিলেন।
ভীষ্মের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ভীষ্ম তাঁকে দ্রুপদের মেয়ে হিসাবে জানতে পেরে অস্ত্র পরিত্যাগ করে শরাক্রান্ত হয়ে শরশয্যায় শায়িত হন এবং মৃত্যুবরণ করেন। যুদ্ধের অষ্টাদশ দিনে অশ্বত্থামার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শিখণ্ডী মৃত্যুবরণ করেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শিখণ্ডীর জন্মরহস্য জানতেন বলে ভীষ্ম দুর্যোধনকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, শিখণ্ডীর বিরুদ্ধে তিনি অস্ত্র ধারণ করবেন না পাণ্ডবরাও তা জানতেন। শিখণ্ডী নিজেও ভালো যোদ্ধা ছিলেন না। তাই শিখণ্ডীকে সামনে রেখে অর্জুন ভীষ্মকে বাণহত করে শরশয্যায় শুইয়েছিলেন। এক্ষেত্রে একমাত্র শিখণ্ডীর ক্ষেত্রেই বলা যায়, নারীশরীর থেকে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। শিখণ্ডীকে অবশ্যই রূপান্তরকামী বলা যায়।
হিন্দু পুরাণে এলজিবিটির বিষয়বস্তু বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। কয়েকজন দেবদেবী ও যোদ্ধাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা আচরণে স্ত্রী সমকামিতা, পুরুষ সমকামিতা, উভকামিতা বা রূপান্তকামিতা (এককথায় এলজিবিটি) অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য ও আচরণে পরিদৃষ্ট হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁদের চরিত্রে লিঙ্গ পার্থক্য ও অ-বিষমকামী যৌনপ্রবৃত্তিরও আভাস মেলে। ঐতিহ্যগতভাবে হিন্দু সাহিত্যে সরাসরি সমকামিতার কথা উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণগুলিতে এবং লোকসাহিত্যে লিঙ্গ পরিবর্তন, সমকামোদ্দীপক (হোমো ইরোটিক) ঘটনা এবং আন্তঃলিঙ্গ ও তৃতীয় লিঙ্গ চরিত্রের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।
হিন্দু পুরাণে দেখা যায় দেবদেবীরা লিঙ্গ পরিবর্তন করছেন বা বিভিন্ন সময়ে বিপরীত লিঙ্গের রূপ ধারণ করছে, অথবা একজন দেবতা ও একজন দেবী মিলিত হয়ে একই শরীরে উভলিঙ্গ রূপ ধারণ করেছে। যৌনমিলনের সুবিধার্থে দেবতাদের বিপরীত লিঙ্গের অবতার রূপে অবতীর্ণও দেখা যায়।
হিন্দু পুরাণগুলিতে আমরা বিষ্ণু ও শিবকে নারীরূপে পাই। হিন্দুধর্মে ও ভারতীয় পুরাণে একাধিক দেবদেবীকে বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন রূপে পুরুষ ও নারী উভয় সত্ত্বা ধারণ করতে দেখা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে আবার একজন দেবতা ও একজন দেবী একই সময়ে একই মূর্তিতে একাধারে পুরুষ ও নারী রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। এইরকম একটি মূর্তি আমরা পাই শিবের অর্ধনারীশ্বর রূপ। এই রূপ শিব ও পার্বতীর সম্মিলিত রূপ। শিবের এই মূর্তিটি দ্বৈতসত্ত্বার উৰ্বেস্থিত সামগ্রিকতার প্রতীক। এই মূর্তি নশ্বর জীব ও অমর দেবদেবীর এবং পুরুষ ও নারীসত্ত্বার যোগসূত্র। এই প্রসঙ্গে অ্যালাই ড্যানিলোর মতে– “উভলিঙ্গ, সমকামী ও রূপান্তকামিতার একটি প্রতীকী মূল্য আছে এবং এঁদের সম্মানীয় সত্ত্বা অর্ধনারীশ্বর মূর্তি মনে করা হয়। আর-একটি অনুরূপ মূর্তি হল লক্ষ্মী-নারায়ণ। এই মূর্তিটি সৌন্দর্য ও সম্পদের দেবী লক্ষ্মী ও তাঁর স্বামী বিষ্ণুর যুগল উভলিঙ্গ মূর্তি।
ভাগবত পুরাণে পাওয়া যায় বিষ্ণু অসুরদের অমৃতের অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য ছলনাকারিণী মোহিনী রূপ গ্রহণ করেছিলেন। শিব মোহিনীকে দেখে আকৃষ্ট হন এবং এর ফলে তাঁর বীর্যস্খলন হয়ে যায়। সেই বীর্য পাথরের উপর পড়ে সোনায় পরিণত হয়। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ গ্রন্থে দেখা যায়, শিবের পত্নী পার্বতী তাঁর স্বামীকে মোহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হতে দেখে লজ্জায় মাথা নত করে ফেলেন। কোনো কোনো উপাখ্যানে দেখা যায়, শিব পুনরায় বিষ্ণুকে মোহিনী রূপ ধারণ করতে বলেন, যাতে তিনি প্রকৃত রূপান্তরটি স্বচক্ষে দেখতে পারেন। যেসব উপাখ্যানে শিব মোহিনীর সত্য প্রকৃতিটি জানতেন, সেই উপাখ্যানগুলিকে যৌন-আকর্ষণে লিঙ্গের অনিশ্চয়তার পরিচায়ক হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়। মোহিনীর নারীসত্ত্বা হল সত্যের জাগতিক দিক। শিবকে আকর্ষিত করার যে চেষ্টা মোহিনী করেছিলেন, তা শুধুমাত্র শিবকে জাগতিক বিষয়ে আগ্রহী করে তোলার জন্যেই। পট্টনায়ক একটি উপাখ্যানের উদাহরণ দেখিয়ে বলেছেন যে, কেবলমাত্র বিষ্ণুরই শিবকে ‘মোহিত’ করার ক্ষমতা ছিল।
এক অসুর নারীমূর্তি নারীমূর্তি ধারণ করে শিবকে হত্যা করতে যায় বলে একটি আখ্যান পাওয়া যায়। সে তাঁর নারীমূর্তির যোনিতে তীক্ষ্ণ দাঁত স্থাপন করেছিল। শিব তাঁর ছলনা ধরে ফেলেন এবং নিজের পুরুষত্ব’-এ একটি ‘বজ’ স্থাপন করে ‘রতিক্রিয়া’-র সময় সেই অসুরকে হত্যা করেন। মহাভারত মহাকাব্যের তামিল সংস্করণ অনুসারে বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ মোহিনীমূর্তি ধারণ করে ইরাবানকে বিয়ে করেছিলেন। ইরাবান আত্মবলিদানের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেন। মৃত্যুর পূর্বে তাঁকে প্রেমের স্পর্শ দান করার জন্য কৃষ্ণ তাঁকে বিয়ে করেন। ইরাবানের মৃত্যুর পর কৃষ্ণ মোহিনীমূর্তিতেই তাঁর জন্য বিলাপ করতে থাকেন। বার্ষিক তালি অনুষ্ঠানে ইরাবানের বিয়ে ও মৃত্যুর ঘটনাকে স্মরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানের হিজড়ারা কৃষ্ণ-মোহিনীর ভূমিকায় অভিনয় করে একটি গণবিবাহ অনুষ্ঠানে ইরাবানকে বিয়ে করেন। এই উৎসব ১৮ দিন ধরে চলে। উৎসব শেষ হয় ইরাবানের আনুষ্ঠানের সমাধিদানের মধ্য দিয়ে। এইসময় হিজড়ারা তামিল প্রথা অনুসারে নৃত্য করতে করতে বুক চাপড়ায়, হাতের চুরি ভেঙে ফেলে এবং বৈধব্যের শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে। পদ্মপুরাণ অনুসারে কৃষ্ণের রাসনৃত্যে কেবলমাত্র নারীরই প্রবেশাধিকার ছিল। সেই রাসনৃত্যে অংশগ্রহণের অনুরোধ জানালে অর্জুন শারীরিকভাবেই নারীতে পরিণত হয়েছিলেন বলে ভিত্তিহীন গল্প ফাঁদা হয়েছে।
আর-একটি উপাখ্যান থেকে জানা যায়, তা হল ইলার কাহিনি। এই কাহিনিটি একাধিক হিন্দু ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায়। ইলা ছিলেন এক রাজা। তিনি শিব ও পার্বতীর অভিশাপে এক মাস পুরুষ রূপে এবং পরবর্তী এক মাস নারী রূপে দেহধারণ করে জীবনযাপন করতেন। লিঙ্গ পরিবর্তনের পর ইলা তাঁর পূর্বের লিঙ্গাবস্থার জীবন বিস্মৃত হতেন। এইরকম এক পর্যায়ে ইলা গ্রহদেবতা বুধকে বিয়ে করেন। ইলার লিঙ্গ পরিবর্তনশীলতার কথা বুধ জানতেন। কিন্তু তিনি ‘পুরুষবেশী’ ইলাকে সেটা জানালেন না। ইলাও তাঁর নারীরূপের কথা ভুলে গেলেন। ইলা যখন নারীরূপে থাকতেন, তখনই বুধ ও ইলা স্বামী-স্ত্রী হিসাবে সহবাস করতেন। রামায়ণ অনুসারে বুধের ঔরসে ইলা এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। যদিও মহাভারত অনুসারে ইলাকেই সেই পুত্রের মাতা ও পিতা বলা হয়েছে। পুত্রের জন্মের পর ইলার অভিশাপের নিষ্পত্তি হয়। এরপর ইলা পাকাপাকিভাবে পুরুষে পরিণত হয়। এরপর ইলা তাঁর স্ত্রীর কাছে ফিরে যান এবং একাধিক সন্তানের জন্ম দেন।
কৃষ্ণের পুত্র শাম্ব। শাম্ব নারীর বস্ত্র পরিধান করে মানুষকে উপহাস করতেন এবং বিপথে চালনা করতেন। নারীর বেশ ধারণ করে তিনি সহজেই নারীদের সঙ্গে অবলীলায় পারতেন এবং তাঁদের সঙ্গে সম্ভোগ করতেন। মৌষলপুরাণ গ্রন্থে দেখা যায়, শাম্ব একবার নারীর বেশ ধারণ করে কয়েকজন ঋষিকে নিজের নিজের গর্ভধারণ নিয়ে প্রশ্ন করেন। ঋষিরা তখন তাঁকে অভিশাপ দেন– পুরুষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি লৌহমুষল প্রসব করবেন।
সুশ্রুতসংহিতায় দুই ধরনের পুরুষ সমকামিতার কথা উল্লেখ আছে। একটি গোষ্ঠীর নাম ‘কুম্ভীক’, যাঁরা পায়ুসঙ্গমে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। অপর গোষ্ঠীর নাম ‘অশ্য’, পায়ুসঙ্গমে যাঁরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। অগ্নি ও সোম দুজনেই পুরুষ দেবতা। এই দুই পুরুষদেবতার মধ্যে সমকামী সম্পর্ক ছিল বলে জানা যায়। এক কাহিনিতে পাচ্ছি অগ্নিদেবতা সোমের বীর্য মুখে ধারণ করছেন। বৈদিক-দেবতা মিত্র ও বরুণের অযোনিজ কামে লিপ্ত হয়ে সন্তান উৎপাদন করেছিলেন। অতএব এখানেও সমকামী সম্পর্কের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। রামচন্দ্রের পূর্বপুরুষ রাজা দিলীপের দুই স্ত্রীর মধ্যেও সমকামী সম্পর্ক ছিল। গণেশের নানা ধরনের জন্মবৃত্তান্তের কথা জানা যায়। তার মধ্যে একটি হল পার্বতী ও গজানো রাক্ষসী নামের দুই নারীর যৌনমিলনের ফলে গণেশের জন্ম হয়।
কেবল সমকামীই নয়, রূপান্তরকামিতারও কিছু উল্লেখ পাই। মহাভারতের কাহিনিতে আমরা অর্জুনের এক স্নান করার কথা জেনেছি, সেখানে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পবিত্র সরোবরে স্নান করতে বলেছিলেন। অর্জুন সেই পবিত্র সরোবরে যেই-না স্নান করলেন, অমনি অপরূপা সুন্দরী এক নারীতে পরিণত হলেন। অর্থাৎ পুরুষ থেকে নারীতে রূপান্তর। সেই রূপান্তরিত নারীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কামকেলির আখ্যান পাওয়া যায়। কেলি শেষে পুনরায় সরোবরে স্নান সেরে অর্জুন পুরুষজীবনে ফিরে আসে। রূপান্তরকামিতার আরও একটি কাহিনিতে পাচ্ছি রাজা ভগ্নাস্বনকে। রাজা ভগ্নাসন সরোবরে স্নান করে পুরুষ থেকে নারীত্ব লাভ করেন এবং তাপসের স্ত্রী হয়ে পুত্রসন্তানও উৎপাদন করেন। পুরাণগুলিতে রূপান্তরকামীরা সন্তান উৎপাদন করলেও বাস্তবে সেটা সম্ভব নয়। এখন পর্যন্ত চিকিৎসা বিজ্ঞান যতটা এগিয়েছে, তাতে কোনো রূপান্তরিত মানুষ গর্ভবতী হতে পারবে ন বা জন্ম দিতে পারবে না। অর্থাৎ কোনো পুরুষ নারীতে রূপান্তরিত হয়ে যেমন গর্ভবতী হতে পারবে না, তেমনি কোনো নারী পুরুষে রূপান্তরিত হয়ে কোনো নারীকে মা করতে সক্ষম হবে না।
হিন্দুসমাজে তথাকথিত হিজড়ারা ব্রাত্য, ঘৃণ্য, প্রান্তিক। তাঁদের সম্মানের চোখে দেখা হয় না। এঁদের নিয়ে খিল্লি করা যায়, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা যায়। এঁরা হাসির খোরাক। তাই এঁরা সমাজের মূল্যস্রোতকে এড়িয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে নিজস্ব কমিউনিটিতে। পুরুষদের উৎপাত এড়াতে এঁরা ট্রেনের লেডিস কম্পার্টমেন্টে রেলভ্রমণ করেন। অবশ্য এঁরা নিজেদের মহিলা ভাবেন বলেই স্বভাবত লেডিস কম্পার্টমেন্ট, লেডিস টয়লেট ব্যবহার করেন। তবে যেসব মহিলারা নিজেদেরকে পুরুষ সত্ত্বার (নারী হিজড়া) অধিকারী ভাবেন, তাঁদের কখনো জেন্টস টয়লেট ব্যবহার করতে দেখা যায় না।
হিন্দুসমাজের অনেকেই মনে করে হিজড়াদের প্রথম মুখদর্শন অশুভ, অমঙ্গলের। হিজড়াদের জন্ম অভিশাপের জন্ম বলে মনে করা হয়। বাচ্চা নাচানো হিজড়ারাও তাঁদের গানে ‘আমাদের জীবন অভিশাপের’ বলেন। এই অভিশাপের সূত্রপাত সম্ভবত মহাভারতে। যেখানে উর্বশীর অভিশাপে অর্জুন এক ‘ক্লীব’ বা তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিতে হয়েছেন। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন যে, পাণ্ডবদের বর্ষব্যাপী অজ্ঞাতবাসের ক্ষেত্রে এই অসুখ ফলপ্রসূ হবে। আবার অনেক ব্যবসায়ীরা মনে করেন সকাল খুলেই হিজড়া প্রথম কাস্টমার হলেই সেদিন ব্যাবসা ভালো হবে।
.
খ্রিস্টান ধর্মে হিজড়া
গ্রিক Eunochos থেকে Eunuchs শব্দটি এসেছে। খ্রিস্টধর্মের নিউ টেস্টামেন্টে স্পষ্ট করে তৃতীয় লিঙ্গ ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে। যদিও এখানে Eunuchs বলতে নপুংসক ব্যক্তি বোঝানো হয়েছে। বিবাহ এবং বিচ্ছেদ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় জিশু বলেন, কিছু মানুষ জন্ম থেকেই Eunuchs, আবার কিছু মানুষ অন্যদের দ্বারা Eunuchs–এ পরিণত হয় এবং আরও কিছু মানুষ আছে যারা স্বর্গরাজ্যের জন্য নিজদেরকে Eunuchs-এ রূপান্তরিত করে।
২০০০ সালে ক্যাথলিক সম্মেলনের ডকট্রিন অফ ফেইথের উপসংহারে বলা হয়, চার্চের দৃষ্টিতে একজন মানুষ ট্রান্সসেক্সয়াল সার্জিকাল অপারেশনের মাধ্যমে একজন মানুষকে শুধু বাহ্যিকভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব পরিবর্তন করা সম্ভব হয় না। “the transsexual surgical operation is so superficial and external that it does not change the personality. If the person was a male, he remains male. If she was female, she remains female.” খ্রিস্টান ধর্মে একজন ইথিওপিয়ান ইনুখ সম্পর্কে আলোচনার কথা আছে। বিবাহ এবং তালাক নিয়ে উত্তর দেওয়ার সময় জিশু এক পর্যায়ে বলেন, “কিছু মানুষ আছে যারা জন্ম থেকে ইনুখ এবং আরও কিছু মানুষ আছে যাদেরকে অন্যেরা ইমুখ বানিয়েছে এবং আরও এক প্রকৃতির মানুষ আছে যারা স্বর্গরাজ্যের জন্য নিজেদেরকেই ইমুখ বানিয়েছে।”
.
বৌদ্ধ ধর্মে হিজড়া
অধিকাংশ বৌদ্ধলিপিতে ধর্ম প্রতিপালনে কোনো লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন করা হয়নি। নির্বাণ লাভের জন্য কামনাকে এই শাস্ত্রে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। থাই বৌদ্ধধর্মে ‘কতি’ বলে একটি শব্দ আছে। মেয়েদের মতো আচরণকারী পুরুষকে ‘কতি’ বলা হয়। এটা সেখানে পুরুষ সমকামীদের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়। থাইল্যান্ডে কতিদের বিবাহের অনুমতি নেই। তাঁরা কখনোই বিয়ে করতে পারবে না। থাইল্যান্ডে কতিদের নারীতে রূপান্তরিত হওয়া কি পুরুষ বিয়ে করা এখনও আইনত অবৈধ। কিন্তু হিজড়া মহিলারা তাঁদের ইউরোপীয় সঙ্গীকে বিয়ে করতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে তাঁকে থাইল্যান্ড ত্যাগ করে তাঁদের সঙ্গীদের দেশে চলে যেতে হবে।
.
ইহুদি ধর্মে হিজড়া
মোজেস বা হজরত মুসার অনুসারীদেরকে বলা হয় ইহুদি। ইহুদি ধর্মে হিজড়া বা ট্রান্সজেন্ডারদের ‘সারিস’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। হিব্রু ‘সারিস’ ইংরেজিতে অনুবাদ করা হয়েছে ‘Eunuch’ অথবা ‘Chamberlain’ নামে। “তনখ’-এ সারিস শব্দটি ৪৫ বার পাওয়া যায়। সারিস বলতে একজন লিঙ্গ নিরপেক্ষ বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি শক্তিমানের প্রতিনিধিত্ব করেন। ঈশ্বর সারিসদের কাছে এই বলে প্রতিজ্ঞা করছেন, “তারা যদি সাবাথ পালন করে এবং রোজা রাখে তাহলে তাদের জন্য স্বর্গে একটি উত্তম মনুমেন্ট তৈরি করবেন।” (ইসাইয়াহ, ৫৬)। “তোরাহ”-তে ক্রস ড্রেসিং (যেমন পুরুষের নারীর মতো পোশাক পরা) এবং জেনিটাল বা শুক্রাশয় ক্ষতিগ্রস্ত করার ব্যাপারে নির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞার কথা বলা হয়েছে। সেজন্য অনেক ইহুদি হিজড়াদের ধর্মের বাইরের মানুষ মনে করেন। কারণ হিজড়ারা বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের কল্যাণে হিজড়ারা তাদের লিঙ্গ পরিবর্তন করে নারী অথবা পুরুষে নিজেদের রূপান্তর করে নিতে পারবেন। ইহুদিধর্মের অনেক শাখা বিজ্ঞানের এই অগ্রগতিকে স্বাগত জানালেও জুদাইজমের সকল ধারা এই রূপান্তরকামিতাকে এখনও সমর্থন করেনি।
.
বাহাই ধর্মে হিজড়া
বাহাই ধর্মবিশ্বাসে হিজড়াদেরকে Sex Reassignment Surgery (SRS) এর মাধ্যমে একটি লিঙ্গ বেছে নিতে হবে এবং শল্যচিকিৎসকের মাধ্যমে লিঙ্গ রূপান্তর করতে হবে। এসআরএসের পরে তাদেরকে রূপান্তরিত বলে গণ্য করা হবে এবং তারা উপযুক্ত সঙ্গী নির্বাচন করে বাহাই মতে বিবাহ করতে পারবে।
প্রধান ধর্মগুলিতে হিজড়াদের অবস্থান সম্বন্ধে মোটামুটি আলোচনা করা গেল যতটুকু জানা গেছে। তবে সমকামীদের ভূগোল-ইতিহাস-বিজ্ঞান সবই দেখে নিতে হবে। না-হলে এই গোষ্ঠীকে সঠিক অনুধাবন করা যাবে না। প্রাচীন যুগে হেরোডোটাস, প্লেটো, অ্যাথেনেউস, জেনোফোন এবং অন্যান্য লেখকদের লেখা থেকে প্রাচীন গ্রিসে সমকামিতা প্রসঙ্গে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়। জানা যায়, প্রাচীন গ্রিসে বহুল প্রচলিত ও সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সমকামী যৌন সম্পর্কটি ছিল প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও সদ্য কিশোর বা পূর্ণকিশোর বালকদের মধ্যেকার যৌন সম্পর্ক (প্রাচীন গ্রিসের বিবাহ প্রথাও ছিল বয়সভিত্তিক; তিরিশ বছর পার করা পুরুষেরা সদ্য কিশোরীদের বিয়ে করত।)। নারীর সমকামিতার বিষয়টি প্রাচীন গ্রিসে ঠিক কী চোখে দেখা হত, তা স্পষ্ট নয়। তবে নারীর সমকামিতাও যে স্যাফোর যুগ থেকে গ্রিসে প্রচলিত ছিল, তা জানা যায়। বিগত শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সমাজে যৌনপ্রবৃত্তিকে যেমন সামাজিক পরিচিতির মাপকাঠি হিসাবে দেখা হলেও, প্রাচীন গ্রিসে তেমনটা হত না। গ্রিক সমাজে যৌন কামনা বা আচরণকে সঙ্গমকারীদের লিঙ্গ অনুযায়ী ভাগ করে দেখা হত না; দেখা হত যৌনক্রিয়ার সময় সঙ্গমকারীরা কে নিজের পুরুষাঙ্গ সঙ্গীর দেহে প্রবেশ করাচ্ছে, বা সঙ্গীর পুরুষাঙ্গ নিজের শরীরে গ্রহণ করছে, তার ভিত্তিতে। এই দাতা/গ্রহীতা বিভেদটি সামাজিক ক্ষেত্রে কর্তৃত্বকারী ও শাসিতের ভূমিকা নিত। অপরের শরীরে পুরুষাঙ্গ প্রবেশ করানো পৌরুষ, উচ্চ সামাজিক মর্যাদা ও প্রাপ্তবয়স্কতার প্রতীক ছিল। অপরদিকে অন্যের পুরুষাঙ্গ নিজের শরীরে গ্রহণ করা ছিল নারীত্ব, এঁরা নিম্ন সামাজিক মর্যাদা ও অপ্রাপ্তবয়স্কতার প্রতীক।
প্রাচীন নাগরিক সমাজ, ব্যক্তির স্বাধীনতা, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ধারণা জন্ম নিয়েছিল গ্রিসে। সেই গ্রিস, যাঁরা কখনো নাগরিকের যৌন স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেনি। সমলিঙ্গ যৌন-সংসর্গ নিয়ে তাঁদের মধ্যে কোনো প্রশ্নচিহ্ন ছিল না কোনোদিন। প্রাচীন গ্রিসের সংস্কৃতিতে প্রথম প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে গভীর প্রণয় সম্পর্কের উল্লেখ পাওয়া যায় ইলিয়াড মহাকাব্যে। রচয়িতা হোমার অ্যাকিলিস ও প্যাট্রোক্ল্যাসের সম্পর্কটিকে যৌন-সম্পর্ক বলেননি। চিত্রকলা ও পাত্রচিত্রে প্যাট্রোক্ল্যাসের দাড়ি আঁকা হত। অপরদিকে গ্রিক সমাজে অ্যাকিলিসের স্থান দেবতুল্য হলেও তাঁর চিত্র উলঙ্গই আঁকা হত। এর ফলে কে ‘এরাস্টেস’ এবং কে ‘এরোমেনোস’ ছিলেন, তাই নিয়ে মতানৈক্য দেখা যায়। হোমারীয় ঐতিহ্যে প্যাট্রোক্ল্যাস ছিলেন বয়সে বড়ো; কিন্তু অ্যাকিলিস ছিলেন বেশি শক্তিশালী। অন্যান্য প্রাচীন গল্পের মতে, অ্যাকিলিস ও প্যাট্রোক্ল্যাস ছিলেন নিছক বন্ধু। ঐতিহাসিক প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ প্রণয়ীযুগলের মধ্যে এথেন্সের পাউসানিয়াস ও ট্র্যাজিক কবি আগাথন বিখ্যাত। আগাথনের বয়স ছিল ত্রিশের বেশি। মহামতি আলেকজান্ডার ও তাঁর বাল্যবন্ধু হেফাস্টনের সম্পর্কও একই ধরনের ছিল বলে মনে করা হয়।
স্যাফো নারী ও বালিকাদের উদ্দেশ্য করে অনেকগুলি কবিতা রচনা করেছিলেন। ইনি লেসবোস দ্বীপের বাসিন্দা। স্যাফো সম্ভবত ১২,০০০ লাইনের কবিতা লিখেছিলেন নারীদের জন্য। তবে তার মধ্যে মাত্র ৬০০ লাইনেরই সন্ধান পাওয়া গেছে। এই মহিলা কবির লেখার পরতে পরতে ছিল নারী-শরীরের বন্দনা। তাই স্যাফো প্রাচীনকালের নারী-সমকামী কবি হিসাবে পরিচিত। তিনি গ্রিক সমাজে ‘থিয়াসোস’ বা অল্পশিক্ষিতা নারী হিসাবে পরিচিত ছিলেন। সে যুগের সমাজে নারীজাতির মধ্যেও সমকামিতার প্রচলন ছিল। নগররাষ্ট্রের উদ্ভবের পর বিবাহপ্রথা সমাজ ও সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে ওঠে এবং মেয়েরা গৃহবন্দি হয়ে পড়ে। থিয়াসসাস’-রা হারিয়ে যায়। স্যাফোর জন্মস্থান লেসবস থেকেই তো অভিধানে জায়গা পেয়েছে ‘লেসবিয়ান’ শব্দটি। সামাজিকভাবে নারীর সমকামিতার কোনো স্থান হয়নি। সাধারণভাবে নারীর সমকামিতার ঐতিহাসিক প্রামাণ্য তথ্য বেশি নেই।
সমকামী বিষয়বস্তু সম্পর্কে দীর্ঘকাল নীরব থাকার পর ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন। এরিক বেথে ১৯০৭ সালে এ বিষয়ে আলোচনা শুরু করেছিলেন। পরে কে, জিডোভারাও গবেষণা চালিয়ে যান। গবেষণায় জানা গেছে, প্রাচীন গ্রিসে সমকামিতার খোলাখুলি প্রচলন ছিল। এমনকি সরকারি অনুমোদনও ছিল। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকে রোমান যুগ পর্যন্ত এই অবস্থা চলেছিল। কোনো কোনো গবেষকদের মতে সমকামী সম্পর্ক, বিশেষত পেডেরাস্টির প্রচলন ছিল উচ্চবিত্ত সমাজের মধ্যেই। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই প্রথার প্রচলন খুব একটা ছিল না। ব্রুস থর্নটনের মতে, অ্যারিস্টোফেনিসের কৌতুক নাটকগুলিতে গ্রহীতার স্থান গ্রহণকারী সমকামীদের প্রতি উপহাস করার প্রবণতা থেকে বোঝা যায়, পুরুষ সমকামিতাকে সাধারণ মানুষ ভালো চোখে দেখত না। ভিক্টোরিয়া ওল প্রমুখ অন্যান্য ঐতিহাসিকেরা বলেছেন, এথেন্সে সমকামী সম্পর্ক ছিল ‘গণতন্ত্রের যৌন আদর্শ। এটি উচবিত্ত ও সাধারণ মানুষ— উভয় সমাজেই সমাজভাবে প্রচলিত ছিল। হার্মোডিয়াস ও অ্যারিস্টোগেইটন নামে দুই হত্যাকারীর ঘটনা থেকে তা প্রমাণিত হয়। এমনকি যাঁরা বলেন যে, পেডেরাস্টি উচ্চবিত্ত সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাঁরাও মনে করেন যে এটি ছিল ‘নগররাষ্ট্রের সামাজিক কাঠামোর অঙ্গ’।
আধুনিক গ্রিসে এই বিষয়ে বিতর্ক হয়েছে। ২০০২ সালে মহামতি আলেকজান্ডার সম্পর্কিত এক সম্মেলনে তাঁর সমকামিতা নিয়ে বিতর্ক হয়। ২০০৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘আলেকজান্ডার’ চলচ্চিত্রে আলেকজান্ডারকে উভকামী হিসাবে দেখানোর জন্য ২৫ জন গ্রিক আইনজীবী চলচ্চিত্রের নির্মাতাদের বিরুদ্ধে মামলা করার হুমকি দিয়েছিলেন। তবে ছবির এক আগাম প্রদর্শনীর পর তাঁরা আর মামলা করেননি।
.
সাহিত্য ও সিনেমায় সমকামী
আধুনিক সাহিত্য-সিনেমাতেও বারবার জায়গা করে নিয়েছে সমকামী মানুষের গল্প। অতীত ও বর্তমান কোনোকালেই সমকামিতাকে অস্বীকার করার উপায় না থাকলেও রক্ষণশীল সমাজ ও পরিবারের বাধা তো ছিলই, আজও আছে। তাই সাহিত্যের দিকে তাকালে তার পরিসরের ক্ষেত্রকে খুব সীমাবদ্ধ বলে মনে হয়েছে। তবু, সাহিত্যে যা নিদর্শন পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে কোনোমতেই অস্বীকার করা যায় না এর অন্তরালে থাকা মনস্তাত্ত্বিক কিছু প্রবৃত্তিকে। এছাড়া শারীরিক কিছু কারণ তো আছেই। ইংরেজি সাহিত্যে ক্রিস্টোফার মার্লোর ‘Edward the Second’ এবং মহেশ দত্তানির ‘Bravely fought the Queen’ নাটক বর্তমান সমাজেও বহু আলোচিত। জগদীশ গুপ্তের গল্পে সমকামিতার আভাস পাওয়া যায় মাত্র। একটি গল্পে রাণুর স্বামীর বদলিজনিত কারণে অন্যত্র যেতে হবে। যাওয়ার আগে কানুর স্ত্রীর ইন্দিরার সঙ্গে রাণু একরাত্রি কাটাতে চায়। তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে আসে সেই অমোঘ কথাগুলি– “তুই আর আমি এক হয়ে যাই”। এক পুরুষের শরীরে এক নারীর এক হয়ে যাওয়াটাকে যেমন বিষমকামিতা বলা হয়, তেমনি এক নারীর শরীরের সঙ্গে আর-এক নারীর এক হয়ে যাওয়াটাকে সমকামিতা বলা হয়। মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে রূপ ছাপিয়ে ইন্দিরার অঙ্গসান্নিধ্যে। রূপ নয়, অরূপের মধ্যে দিয়ে নিজেকে স্বামী আর ইন্দিরাকে স্ত্রী ভেবে মিলনেচ্ছায় রাণু বলেই ফেলে সেই ইচ্ছের কথা। ইন্দিরার মুখে শুনি –“যেন স্বামী আর স্ত্রী, সে আর আমি”। কমলকুমার মজুমদারের মল্লিকা বাহার’ কাহিনিতে সমকামিতার আভাস মেলে। মল্লিকার পুরুষ-সঙ্গের অভাব তাঁর যৌন-তাড়নার অভিমুখ বদলে যায়। তাই শোভনাদির সঙ্গে যখন দেখা হয় তখন থেকেই সম্পর্ক গড়ে ওঠে দুই নারীর। লেখকের ভাষায়– “শোভনার চোখে অন্য আলো এসে পড়েছে, তাঁর চোখে-মুখে দেখা যাবে পুরুষালি দীপ্তি, যে-কোনো রমণী যে সে ঘাটের পথে, বাটের পথে চিকের আড়াল হতে দেখুক, ভালো এ দৃষ্টি লাগবেই… শোভনার স্পর্শের মধ্যে কেমন এক দিব্য উষ্ণতা, এ উষ্ণতা বহুকাল বয়সি বহুজন প্রিয়। মল্লিকার এ উষ্ণতা ভালো লেগেছিল, ভারী ভালো লেগেছিল।” মল্লিকার মন সায় দিয়েছিল, তাই অন্তর থেকে সে স্পর্শসুখকাতরতা অনুভব করেছিল। সেই কাতরতা অনুভব করেছিল বলেই শোভনার সঙ্গে সে তাঁদের বাড়ির ছাদে যায় নিভৃতে কিছুক্ষণ সময় কাটাতে। সেখানে শোভনার আচরণের মধ্যেও পুরুষালি ভাব প্রকট হয়। লেখক বলছেন –“শোভনা আপনার মধ্যে মল্লিকাকে এনেছে, সোহাগ করে মালা পরিয়ে দিয়েছে, সে মালা তাঁর কণ্ঠে বিলম্বিত, চুম্বনে চুম্বনে শোক ভুলিয়ে দিয়েছে।” গল্পের শেষ অংশে পাঠকরা পাচ্ছেন সেইসব সাহসী কথোপকথন। শোভনা বলছে –“কই তুমি আমায় খেলে না? তুমি আমায় ভালোবাসো না?” “বাসি!” মল্লিকা শোভনাকে বিশেষ অপটুতার সঙ্গে গভীরভাবে চুম্বন করলে—
“আগে কাউকে কখনো এমনভাবে …”
“হ্যাঁ … আচ্ছা আপনি?”
“আমায় তুমি বলো, আমি তোমার কে? বলো?”
“আচ্ছা তুমি?”
“না”, দৃঢ়কণ্ঠে শোভনা বললে। বোধহয় মিথ্যা। হেসে বললে, “আমি তোমার স্বামী, “তুমি”, “বউ”।” লেখক জানাচ্ছেন, “(এই) শুনে শোভনা আবেগে চুম্বন করলে। শোভনার মুখনিঃসৃত লালা মল্লিকার গালে লাগল।”
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ‘বুটকি ছুটকি’ গল্পেও খুব সংক্ষিপ্তভাবে শেষদিকে এসেছে দুই বোনের স্পর্শজনিত অনুভবের কথা। মাতৃহীন দুই সমবয়সি বোনের জীবনে জীবনে না আছে কোনো আনন্দের কলরব, না আছে কোনো আশার প্রদীপ। ক্রাচ নিয়ে জীবনোপায় অবলম্বন করা দরিদ্র বাবা প্রতাপের বাড়িতে ইলেকট্রিকের আলো কেটে দিয়েছে। প্রাকৃতিক নিয়মে দুই বোন চোদ্দো পনেরোয় যখন পৌঁছোয়, তখন স্বভাবতই পুরুষের দৃষ্টির আওতার বাইরে থাকে না তাঁরা। “বুটকির কোমরের দিকটা সুন্দর। ছুটকির বুকের দিকটা।” টগবগে যৌবনা দুই নারী, দুই বোন পরস্পরের সহমর্মী হয়ে বেঁচে থাকে বাবার ফিরে আসার প্রতীক্ষায়, অনেক গভীর রাত পর্যন্ত। চরম দারিদ্রতা, তাই পরনের অভাবে নিকষ অন্ধকারে তাঁরা নিরাবরণ হয়ে শোয়। এক বোন আর-এক বোনকে দেখে। দেখে নগ্ন শরীর। এক বোন দেখে, “দিদির ঘাড়ের সুন্দর বাঁক। শাঁখের মতন সরু হয়ে নীচের দিকে গড়িয়ে আসা গলা।” অন্য বোন দেখে, “সবুজ আলোটা বল্লমের মতো খোঁচা মেরে ছুটকির সুন্দর উঁচু বুকের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছিল, পাতলা জামার ছিদ্র দিয়ে উদ্ধত স্তনের চূড়ায়। একটা চূড়া বেরিয়ে এসেছিল। বিশেষত ছুটকি যখন বলে, “রক্ষা করো বাবা, দরকার নেই রাজার ছেলের, বিনা পণে যদি বুড়ো মদন এসে তুলে নিয়ে যায় বাঁচি”, তখন বোঝাই যায় কামনা-বাসনার প্রতি লোভাতুর হয়ে আছে অসহায় নারী। না-হলে রাত্রের অন্ধকারে নিরাবরণ দুই বোন দুটি শরীরকে আশ্রয় করে উষ্ণতা চাইবে কেন!
তিলোত্তমা মজুমদারের ‘চাঁদের গায়ে চাঁদ’ উপন্যাসে দেবরূপার শ্রেয়সীর প্রতি সমকামিতার প্রকাশ তাঁকে ক্রমশ বিপন্ন করে তোলে –“শ্রুতি হোমাসেক্সয়াল ঘেন্না করে। শ্রুতি হোমোসেক্সয়াল ভয় পায়।” দেবরূপা শ্রেয়সীর প্রতি আসক্ত, যদিও শ্রেয়সী শুভ্ৰশীলের প্রতি প্রণয়াসক্ত। কিন্তু কাহিনি থেকে জানা যায়, দেবরূপা প্রচণ্ডই পুরুষবিদ্বেষী। তাই সে শ্রেয়সীকে শুভ্ৰশীলের কবল থেকে মুক্ত করতে হয়। আর এই সব কিছুর মূলেই যে তীব্র কামচেতনা তা লেখিকা বুঝিয়েছেন– “তোমাদের মধ্যেও দেখো এই দুই বিভাগ। পীড়ক ও আত্মপীড়ক। কিন্তু দুই-ই স্বাভাবিক। দুই-ই কামবোধের প্রকাশ। দুই-ই প্রকৃতির ইচ্ছা। শুধু বৈচিত্র্য ব্যাপ্ত। নারী নারী, পুরুষ পুরুষ সম্পর্কে ভেদ নেই। কারণ শুধুই মানুষে মানুষে টান সমাজের জন্ম দিয়েছিল। মানুষে মানুষে টান গড়নের জন্ম দেয়।”
বদলেছে মানুষের মানসিকতা, বদলেছে মানুষের প্রান্তিক ধ্যান-ধারণা। তাই পুরস্কৃত হয় স্বপ্নময় চক্রবর্তীর ‘হলদে গোলাপ’। নর-নারীর যৌন সম্পর্ক, সমকামীদের আকাঙ্ক্ষা-যন্ত্রণা, তৃতীয় লিঙ্গ সম্প্রদায়ের বিস্তৃত বিবরণ উপন্যাসটিকে একটি বৈপ্লবিক মাত্রা সংযোজন। সংযোজন বলাটা ভুল হল বোধহয়, আসলে তৃতীয় লিঙ্গ সম্প্রদায়ের কাহিনিই এতে যোজিত হয়েছে। ‘হলদে গোলাপ’ প্রসঙ্গে মনে পড়ে বিচারপতি কে. এস. রাধাকৃষ্ণণের উক্তি : “তৃতীয় লিঙ্গের স্বীকৃতি কোনো সামাজিক বা চিকিৎসা সংক্রান্ত ইস্যু নয়, মানবাধিকারের প্রশ্ন বলেই বিবেচ্য।” এই উপন্যাসে অনিকেত একজন বেতারকর্মী— যিনি সমকামী, লিঙ্গান্তরকামী কিছু মানুষের কথা তুলে ধরেছেন, বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন হিজড়ে সম্প্রদায়ের অন্ধকারময় জীবনের কথা– যৌনতার বিকৃতিজনিত কিছু অসুস্থতার কথা, যাঁদের বর্তমানে এলজিবিটি বলে চিহ্নিত করা হয় তাঁদের জীবনচিত্র। কিন্সের তত্ত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছেন, “প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পুরুষ সত্ত্বা ও নারী সত্ত্বা একসঙ্গে থাকে। সব পুরুষের কম-বেশি সমলিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণ আছে।” তবে শুধু পুরুষরা নয়, নারীরাও সমলিঙ্গে আকর্ষণ বোধ করে। বরং বেশিই। লেখক স্বপ্নময় চক্রবর্তী যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন– বিষমকাম যেমন স্বাভাবিক একটা ব্যাপার, সমকামও তেমনই। তবে মানুষের হরমোনাল একটা ‘স্কেল থাকে। তার তারতম্যেই আসে ‘এলজিবিটি তত্ত্বটি। সুধীর চক্রবর্তী গ্রন্থটির আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন– “আনকমনদের বেদনার্ত আখ্যান”।
তৌহিদুর রহমানের লেখা ‘নীল যমুনার জলে’ উপন্যাস নিয়ে তোলপাড় হয়েছিল। বইমেলায় প্রকাশিত এই উপন্যাসটি নিয়ে প্রতিক্রিয়াশীল বিভিন্ন গোষ্ঠী তাঁদের মতামত– বইটি নিষিদ্ধ করতে হবে। নীল যমুনার জলে’-র কেন্দ্রীয় চরিত্র সোমা। যিনি একজন কলেজ ছাত্রী। আর-একটি চরিত্র রেহানা। তিনি একজন কলেজের শিক্ষিকা। এই দুই চরিত্র ঘিরেই এগিয়েছে উপন্যাসের কাহিনি। এতে দেখানো হয়েছে দুজন একই প্রকৃতির। তাঁদের দুজনেরই পুরুষের কোনো আকর্ষণ নেই। কোনো পুরুষের প্রতি আকর্ষণ না থাকাটাই স্বাভাবিক। তার মানে যৌনতা নেই, তা কিন্তু নয়। সোমা ও রেহানা উভয় উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ খুঁজে পায়। সেই আকর্ষণে থাকে তীব্রতা। কেউ একে অপরকে ছেড়ে থাকতে পারে না। ধীরে ধীরে একসময় দুজন দুজনকে ভালোবেসে ফেলে। দুজনে চলার পথে একসময় বুঝতে পারে আর দশটা মানুষের মতো ওদের জীবন নয়। তাই সিদ্ধান্ত নেয় তাঁরা সারাজীবন একসঙ্গে থাকবে। তবে সামাজিক কারণে ওরা একসঙ্গে থাকতে পারে না। একদিন দুজনেই মালাবদল করে গোপনে বিয়ে করে নিলেন। সে বিয়ের কথা কেউ জানতে পারল না। ওরা কারোকে জানাতেও পারে না। এভাবেই বয়ে চলে দুটি জীবন। লেখক বিশ্বাস করেন, “বাংলাদেশে অনেক সমকামী পুরুষ আছেন। আর থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থার কারণে সমকামী নারী পুরুষরা এখানে নিজেদের আড়ালে রাখেন। সমকামিতা কোনো প্রকৃতিবিরুদ্ধ আচরণ নয়, বরং খুব স্বাভাবিক।”
শুধু গল্প-উপন্যাসেই নয়, সমকাম ধরা দিয়েছে কবিতাতেও। এই সময়ের কবি অনুপম মুখোপাধ্যায় লিখছেন –
“আমার খবর জবাব নেই। কুসুমের কাছে
বাগান আমাকে এখানে। এই। নোটিশ দিয়েছে।
বোঁটা জানে, ডাল জানে। মালি নই আমি
বেতন দিয়েছে। শুধু। পরাগ দিল না।
হায়ের বয়স কত। কেউ কি তা জানে
এতদিন। ছায়া সে তো রোদেই ফেলেছে।
ধুলোর অনেক কাছে। রেণু। রাখা ছিল
আমার এলার্জি। তার। ঠিকানা পেল না।
সুগন্ধ এভাবে। বেশ। কেটেই চলেছে
অপর সুগন্ধী। সেই। মনে পড়ে গেল।
কিছু নেই। খুব জানি। কিছুই তো নেই।”
কবি চৈতালী চট্টোপাধ্যায় ‘বান্ধবীবিহার’ কবিতাটিতে লিখছেন –
“ব্যত্যয় নেই কোনও! আমি
জানি, তোকে ভালবাসি, তাই এ-জগত
মধুময় লাগে। আয়োজনে, যদি কিছু
বিরোধিতা জাগে! খুনি বোমা বেঁধে
চলে, কোকিল লুকিয়ে কাঁদে
বসন্তগোড়ায়, দুধে-বিষে মিশে গেলে,
তখন সমাজ, খোলা বাথরুম হয়ে, যায়! … দরোজা দিয়েছি, জানলাও,
আমাদের ঘরে মধুঘুম নামবে, বল
সখি, মম সঙ্গে লিভ-ইন করবে কি।”
কিছুদিন আগে নিজেকে সমকামী দাবি করে একটি গানও লিখেছেন দুই বাংলার জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী কবীর সুমন।
“পুরুষ হও বা নারী, তুমিই আমার সখা”– ঋগ্বেদের এই উক্তিকে পুঁজি করেই ১৪ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল সমকামিতার উপর প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র ‘১০ জুলাই’। এর আগে বিভিন্ন বাংলা চলচ্চিত্রে সমকামিতার আভাস থাকলেও সমকামীদের নিয়ে পূর্ণাঙ্গ কোনো চলচ্চিত্র এটাই প্রথম। সারা দেশে সমকামী প্রেম যেখানে নিষিদ্ধ, সেখানে পরিচালক রাতুল গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্মিত এই ছবির রিলিজ নিয়ে হইচই তো হবেই। ভারতীয় চলচ্চিত্রে বিভিন্ন সময়ে বিষয়বস্তু হিসাবে উঠে এসেছে সমকামিতা। বলিউডে সমকামিতা বিষয়ক কিছু ছবি নিয়ে জি নিউজে একটি প্রতিবেদনে প্রকাশ করেছিল। বম গে’ (১৯৯৬) সমকামিতার উপর তৈরি ভারতের প্রথম ডকুফ্লিম। যদিও ভারতে মুক্তি পায়নি এই ছবি। কবি আর, রাজ রাওয়ের লেখার উপর, মুম্বাইয়ের গে সংস্কৃতি নিয়ে গে পরিচালক রিয়াদ ভিঞ্চি ওয়াদিয়ার ছবিতে অভিনয় করেছিলেন রাহুল বসু। ‘ফায়ার’ (১৯৯৭) ভারতে সমকামী চলচ্চিত্র তৈরির পথপ্রদর্শক দিপা মেহতা। তাঁর ট্রিলজির প্রথম ছবি ‘ফায়ার’। বৈবাহিক জীবনের সমস্যায় জর্জরিত দুই মহিলার শারীরিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার কাহিনি নিয়ে ফায়ার’ ভারত রক্ষণশীল সমাজে আগুন জ্বেলেছিল। বক্স অফিসে মুক্তি রক্ষণশীল সমাজের ভ্রুকুটি এড়াতে পারেনি। এর ছয় বছর পর ‘ম্যাঙ্গো সুফলে’ (২০০২) চলচ্চিত্রটি বানিয়েছিলেন সাহিত্য একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত মহেশ দত্তানি। একাকিত্বে ভোগা গে ফ্যাশন ডিজাইনারের গল্প ব্যঙ্গাত্মক মোড়কে উপস্থাপন করেছিলেন মহেশ। ফায়ারের মতো রক্ষণশীলদের প্রতিবাদের মুখে পড়তে না-হলেও চুপিচুপি মুক্তি পেয়ে চুপিচুপিই প্রেক্ষাগৃহ থেকে চলে গিয়েছিল ম্যাঙ্গো সুফলে।
‘কাল হো না হো’ (২০০৩) চলচ্চিত্র মুম্বাইয়ের মেনস্ট্রিম ধারার সমকামিতাকে ব্যঙ্গাত্মক রূপ দিয়েছিলেন করণ জোহর। তবে শুধু সমকামিতা নয়, সমকামিতার প্রতি সাধারণ মানুষের ভুরু কোঁচকানোও করণ তুলে এনেছিলেন এই চলচ্চিত্রে। শাহরুখ খান ও সইফ আলি খানের গে সম্পর্ক দেখে চমকে ওঠেন ছবির চরিত্র কান্তা বেন। গার্লফ্রেন্ড’ (২০০৪) আর-একটি চলচ্চিত্র। গে সম্পর্ক নিয়ে চলচ্চিত্র বেশ কিছু চলচ্চিত্র তৈরি হলেও লেসবিয়ান সম্পর্ক নিয়ে চলচ্চিত্র ফায়ারের পর হয়েছে গার্লফ্রেন্ড। দুই বন্ধুর মধ্যে একজন লেসবিয়ান, অন্যজন বাই-সেক্সচুয়াল। বন্ধুর সঙ্গে সমকামিতার সম্পর্ক ছাড়াও তাঁর জীবনে ছিল প্রেমও। সমকামিতার সম্পর্ক ও বিষমকামিতা (Heterosexuality) সম্পর্কের দ্বন্দ্ব, বয়ফ্রেন্ড ও বন্ধুর মধ্যে যৌনহিংসা নিয়ে এগিয়েছে গার্লফ্রেন্ডের গল্প। মাই ব্রাদার নিখিল’ (২০০৫) গে পরিচালক ওনির প্রথম চলচ্চিত্রেই গে সমকামিতাকে দারুণ সফলভাবে নিয়ে এসেছিলেন। ভারতের মতো দেশ থেকে সমকামিতার কারণে একঘরে হয়ে যাওয়া থেকে এইডস নিয়ে বাঁধাধরা ধারণা, সর্বোপরি পরিবারের পাশে দাঁড়ানো সবকিছুই ওনির তুলে ধরেছিলেন। পরে ‘আই অ্যাম’ চলচ্চিত্রেও। হানিমুন ট্রাভেলস প্রাইভেট লিমিটেড’ (২০০৭) চলচ্চিত্রে ছয়জন সদ্যবিবাহিত জুটির হনিমুনের গল্প। এই ছয় জোড়ার মধ্যেই ছিলেন একজন বিবাহিত সমকামী পুরুষ। কীভাবে সেখান থেকেই অন্য সমকামী পুরুষের প্রতি আকর্ষণ ও বৈবাহিক সম্পর্কেও নিজেদের নিজেদের পছন্দের জায়গা বেছে নেন তাঁরা। ফ্যাশন’ চলচ্চিত্রে সমকামিতার অন্য দিক তুলে ধরেন মধুর ভাণ্ডারকর। সমাজের সামনে নিজের সমকামিতা লুকিয়ে রাখতে বন্ধু মুগ্ধা গডসেকে বিয়ে করেন গে ডিজাইনার সমীর সোনি। পাঁচ বছর পর আবার একই বিষয়ে ‘দোস্তানা’ চলচ্চিত্রটি রুপোলি পর্দায় নিয়ে আসেন। করণ জোহর। অভিষেক বচ্চন ও জন আব্রাহামের গে সম্পর্ক বক্স অফিসে প্রথমবারের জন্য কিছুটা হলেও দর্শকদের আনুকূল্য পেয়েছিল। পরে ‘বম্বে টকিজ’ চলচ্চিত্রেও সমকামিতা দেখিয়েছেন করণ জোহর। বস্তুত করণ জোহর নিজেও একজন সমকামী ব্যক্তিত্ব। সেই কারণে সুযোগ পেলেই উনি সমকামিতা বিষয়টাকে তাঁর চলচ্চিত্রে টেনে আনেন। ‘ডোন্ট নো হোয়াই না জানে কিউ’ (২০১০) চলচ্চিত্রকেও সেন্সর বোর্ডের চোখ-রাঙানিতে পড়তে হয় সমকামিতা প্রদর্শনের জন্য। এমনকি সমকামিতার দৃশ্যে অভিনয় করার অভিনেতা যুবরাজ পরাশরকে ত্যাজ্য করেছিল তাঁর পরিবার।
দীপা মেহতার ‘ফায়ার’ বা মধুর ভাণ্ডারকারের ‘পেজ থ্রি’ ছাড়াও সমকালে ভারতীয় সিনেমাতে সমলিঙ্গ প্রেমের প্রচুর উদাহরণ আছে। সদ্যপ্রয়াত ঋতুপর্ণ ঘোষের ‘চিত্রাঙ্গদা’, কিংবা ‘তিনকন্যা’, মৈনাকের ফ্যামিলি অ্যালবাম’, অপর্ণা সেনের ‘পারমিতার একদিন’ ‘তাসের দেশ’-এর মতো হাল আমলের নানা বাংলা ছবির গল্পও ঘিরেছে সমকামী সম্পর্ক। লক্ষ করা গেছে, আদিকাল থেকে শিল্প-সাহিত্যে মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত অভিলাষ সমকামিতার প্রতিফলন। একদা যেটা লুকিয়ে-চুরিয়ে হত আজ তা প্রকাশ্যে এসেছে। সমসাময়িক সাহিত্য ও চলচ্চিত্রে বারবার জায়গা করে নিয়েছে সমকামী মানুষের গল্প। হেরোডোটাস, প্লেটোর মতো দার্শনিক-চিন্তাবিদদের লেখায় প্রায়ই পাওয়া যায় সমকামী সম্পর্কের কথা।
তবে সমকামী পুরুষ ও সমকামী নারীরা হলিউডে গুরুত্ব পেলেও বলিউডের চলচ্চিত্রে তাঁদের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। আর বড়ো বাজেটের চলচ্চিত্রে একদমই দেখা যায় না তাঁদেরকে। মিডিয়ায় সমকামী পুরুষ, সমকামী নারী, উভকামী এবং হিজড়াদের উপস্থিতি এবং তাঁদের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিষয়াদি পর্যবেক্ষণ করে ‘গ্লাড’। সংগঠনটির মুখপাত্র উইলসন ক্রুজ জানান, মার্কিন সমাজে এসব চরিত্রের গুরুত্ব থাকলেও হলিউডের বড়ো বাজেটের ছবিতে তাঁদের দেখা যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে পরিবর্তন জরুরি। সামগ্রিকভাবে হলিউড এবং মার্কিন চলচ্চিত্র তারকারা সমকামীদের অধিকারের দাবিতে সোচ্চার হলেও ছবিতে তার প্রতিফলন নেই। ২০১২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ১০১টি বড় বাজেটের ছবির মধ্যে মাত্র ১৪টি পুরুষ বা নারী সমকামী এবং উভকামীদের চরিত্র ছিল।
ইতিহাস বলছে, প্রাচীন পারস্যে সমকামী সম্পর্কের প্রচলন ছিল। এই ভারতবর্ষেও সমকামিতা ছিল এবং আছে। বহু হিন্দু মন্দিরের দেওয়ালের ভাস্কর্য তো সমকামেরই পরিচয় প্রকট হয়ে আছে। খাজুরাহোর শিল্পকীর্তিতে তো রয়েছে গ্রুপ সেক্সের নিদর্শনও। বাৎসায়নের কামসূত্রেও সমকামিতা নিয়ে আলোচিত হয়েছে, দেখানো হয়েছে যৌন সম্পর্কেরই অন্য এক রূপ। অস্কার ওয়াইল্ডের জীবনী লিখতে গিয়ে প্রখ্যাত এই সমকামী সাহিত্যিকের জীবনের নানা দিক তুলে ধরেছেন রিচার্ড এলম্যান।
সমকামীদের বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেক ভুলভাল ধারণা আছে। যেমন—
(১) সমকামিতা পাশ্চাত্যের সৃষ্টি। পাশ্চাত্যের উদার সমাজব্যবস্থা এবং ভোগবাদী দৃষ্টিভঙ্গি সমকামিতার জন্য দায়ী।
(২) সমকামিতা এক ধরনের মানসিক বিকৃতি বা অসুস্থতা।
(৩) সমকামীদের সুশিক্ষা এবং চিকিৎসার মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব।
(৪) সমকামিতা একটা রোগ।
(৫) প্রকৃতিতে অন্য কোনো জীবজন্তু বা গাছপালার মধ্যে সমকামিতা দেখা যায় না।
(৬) সমকামীদের সামাজিকভাবে বয়কট করা উচিত।
(৭) জীবজন্তুরা তো অনেক কিছু করে, তাই বলে সেগুলি মানুষেরও করতে হবে নাকি?
উত্তরে বলি— প্রথমত, সমকামিতা মোটেই পাশ্চাত্যের সৃষ্টি নয়। এটা অত্যন্ত ভুল ধারণা। সমকাম কোনো ফ্যাশন নয় যে, ওখান-এখান থেকে মানুষ গ্রহণ করবে। সমকাম একটি জৈবিক বিষয়, যা শরীর অনুমোদন করে দেশ-কাল নারী-পুরুষ নির্বিশেষে। প্রথমত, আদিমকাল থেকেই সমকামিতা আছে। ইতিহাসের বিভিন্ন অংশে সমকামিতার দৃষ্টান্ত আছে। সমকামিতা কোনো ফ্যাশান নয়, এটি একটি যৌন-সংকট বলা যায়। প্রাচীন বিভিন্ন মহাকাব্য সমকামিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে। মধ্যপ্রাচ্যে সমকামিতার ব্যাপক প্রচলন ছিল এক সময়ে। আলেক্সান্ডার দ্য গ্রেট, সক্রেটিস সমকামী ছিলেন। কামসূত্রে সমকামিতার প্রচুর উদাহরণ আছে। অতএব সমকাম কোনো পাশ্চাত্যের তৈরি করা বিষয় নয়। দ্বিতীয়ত, প্রাণীকুলে সমকামিতার ব্যাপক বিস্তার দেখতে পাওয়া যায়। প্রাণীকুল পাশ্চাত্যের উদার জীবনব্যবস্থা থেকে শিক্ষা নিয়েছে এটা যাঁরা ভাবে তাঁদের সম্পর্কে বলার কিছু নেই।
দ্বিতীয়ত, সমকামিতা কোনোভাবেই মানসিক বিকৃতি নয়। জীববিজ্ঞানী এবং মনোবিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, সমকাম কোনো মানসিক বিকার নয়। এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক প্রাকৃতিক বিষয়। প্রত্যেক জীবের মধ্যে কিছু অংশ অবশ্যই সমকামী হয়ে জন্ম নেবে। তারা বেড়ে উঠবে সমকামী হয়ে, তাদের চালচলনে সমকামী ভাব ফুটে উঠবে। একটা রক্ষণশীল সমাজে সমকামীরা বেঁচে থাকে গোপনে, তাদের যৌনপ্রবৃত্তি তারা উপভোগ করে গোপনে, অনেক ক্ষেত্রে অপরাধের মাধ্যমে, আর-একটা মুক্তসমাজে সেটা হয় প্রকাশ্যে। প্রকাশ্যে হওয়ার কারণে অপরাধের মাত্রা কমে যায়। মাদ্রাসার শিক্ষকদের বিরুদ্ধেও সমকামিতার অভিযোগ শোনা যায়। মাদ্রাসার শিক্ষকরা যাঁরা সমকামী, তাঁরা তাঁদের যৌন আকাঙ্ক্ষা মেটায় অপরাধের মাধ্যমে শিশু ছাত্রদের সঙ্গে। হয়তো তাঁরা একজন নারীর সঙ্গে বিবাহত জীবন পালন করছে, কিন্তু তৃপ্তির অভাবে তাঁরা প্রতিনিয়ত সুযোগ খোঁজে তাঁদের অবদমিত কামনা পুরণের। যার শিকার সব সময় আমাদের দেশের বালক-তরুণরা হয়। অন্যান্য বিদ্যালয়ের সমকামী | শিক্ষক-শিক্ষিকারও যৌনক্ষুধা মিটিয়ে নেয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্য দিয়ে। ব্যাপারটা বেশ গোপনেই চলে। উন্নত বিশ্বে সমকামীরা প্রকাশ্যে বলে যে তাঁরা সমকামী। যার ফলে চিনতে পারা সহজ হয় এবং সমলিঙ্গের Straight মানুষরা সবসময় সতর্ক থাকতে পারে। তার উপর সমকামীরা সমকামী সঙ্গী বেছে নিয়ে স্বাভাবিক বিবাহিত এবং যৌন জীবনযাপন করলে তাঁরা অপরাধের মাধ্যমে তাঁদের যৌনাকাঙ্ক্ষা পূরণ করার প্রয়োজন পড়ে না।
তৃতীয়ত, সমকামীদের নিয়ে যেই মামলাগুলি হয়েছে, সেখানে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা দাবি করেছিল যে সমকামীরা বিকৃতির শিকার কিংবা রোগী বা কিংবা অসুস্থ। কিন্তু মেডিকেল সায়েন্সে বিপরীতকামীদের সঙ্গে সমকামীদের কোনো পার্থক্য আছে, শারীরিক বা মানসিকভাবে, তার কোনো প্রমাণ নেই। তাহলে সমকামীরা অসুস্থ বা মানসিক বিকৃতির শিকার বা বিকলাঙ্গ তাও বলা যাচ্ছে না।
চতুর্থত, প্রকৃতিতে বিভিন্নভাবে কীভাবে সমকামিতা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। প্রকৃতির সৃষ্ট প্রায় প্রতিটি প্রাণী এবং বৃক্ষরাজিতে সমকামিতা বিদ্যমান। বেশিরভাগ জীব এবং গাছপালায় সমকামিতার প্রকাশ আছে।
পঞ্চমত, সমকামীদের কেন সামাজিকভাবে বয়কট করার কথা বলা হবে? তাঁরাও রক্তমাংসের মানুষ। একজন সমকামী পুরুষের নারীর প্রতি প্রাকৃতিকভাবে আকর্ষণ বোধ করে না। কোনো নগ্ন বা অর্ধনগ্ন নারী দেখলে তার লিঙ্গ উত্থিত হয় না। সেই পুরুষের লিঙ্গ উত্থিত হবে কোনো নগ্ন বা অর্ধ নগ্ন পুরুষ দেখলে। একইভাবে নারী সমকামীরও কোনো নগ্ন নারী দেখলে উত্তেজনা আসবে, অপরদিকে পুরুষদের দেখে তাঁকে যৌনসঙ্গী করার কোনো ইচ্ছাই জাগবে না। এই কারণে নিশ্চয়ই একজন মানুষকে একঘরে করে রাখা বা বয়কট করা কোনোমতেই মানবিক আচরণ হতে পারে না। এটা অন্যায্য, ব্যক্তি-স্বাধীনতায় নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ।
ষষ্ঠত, জীবজন্তুরা এমন অনেক কাজ করে যেটা সভ্য মানুষের করা উচিত নয়, এটা ঠিক। যেমন ধর্ষণ প্রবৃত্তি জীবকুলে বিদ্যমান, পিতামাতার সঙ্গে যৌনতা প্রাণীকুলে বিদ্যমান। একজন সভ্য মানুষ কখনোই এই ধরনের কাজ করতে বা সমর্থন করতে পারে না। কথা হচ্ছে সমকামিতাও কি একই ধরনের ব্যাপার?
বিরোধীরা বলেন, সমকাম প্রবৃত্তি প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং সৃষ্টিশীল নয়। তাই সেটা আইনসংগত করার কোনো মানে হয় না। সমাজে অবক্ষয় আসবে। সমকামিতা না থাকলে সমাজের কী ক্ষতি হবে? সমকাম সমাজের বা প্রকৃতির কোন্ উপকারে লাগবে? ইত্যাদি।
আমি বলি– কে বলল সমকামিতা প্রকৃতিবিরুদ্ধ? কোন্ যুক্তিতে? সমকামী মানুষরা কি প্রকৃতি ছাড়াই জন্ম নিয়েছে? নারী ও পুরুষদের মতো সমকামীদেরও এই প্রকৃতি থেকেই জন্ম হয়েছে। নারী ও পুরুষদের মতো সমকামী মানুদের শরীরও তৈরি হয়েছে প্রকৃতির উপাদান দিয়েই। আমরা বিপরীতকামীরা যে উপায়ে যৌনতা করি তার সব ইভেন্টই কি সৃষ্টিশীল? একটা বা দুটো সন্তানের পিতামাতা হওয়া কি প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়? তাহলে তো প্রকৃতিবিরুদ্ধতার অভিযোগে জন্মনিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনাটা বাতিল করতে হয়! জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রকৃতিবিরুদ্ধতা নয়?
আদিম যুগে যে সময় বিবাহ প্রথা ছিল না, যখন মানুষ প্রাণীদের মতোই ভোলা আকাশের নীচে যৌনমিলন করেছে, প্রকৃতির কোলে জন্ম নিয়েছে ও মরেছে, সেটা কী প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল? নাকি বিবাহ প্রথাটাই প্রকৃতিবিরুদ্ধ? যেসব নারী বা যেসব পুরুষ বন্ধ্যা হওয়ার কারণে সন্তানের জন্মদানে অক্ষম, তাঁদের যৌনজীবন কি প্রকৃতিবিরুদ্ধ?
বস্তুত সমকামিতা সমকামীরা নিজে নির্ধারণ করে না। প্রকৃতি তাঁদের ভিতরে সমকামিতার বীজ বপন করে রেখেছে। একজন ধর্ষক ধর্ষণ না-করেও সুস্থ যৌনতার মাধ্যমে নিজের যৌনাকাঙ্ক্ষা পুরণ করতে পারে। একজন ইনসেস্টার বা অজাচারিতা ইনসেস্ট বা অজাচার সম্পর্ক না-করেও সুস্থ যৌনজীবন যাপন করতে পারে। সমকামীরা কীভাবে যৌনজীবন যাপন করবে? এই প্রশ্নটাই মূলত বিপরীতকামীদের মাথার ব্যথার কারণ। যেভাবেই করুক, সেটা তাঁদের ব্যক্তিগত পরিসরেই করে। সমকামীরা কেন তাঁদের রুচিমতো যৌনতা উপভোগ করতে পারবে না? কেন পারবে না?
হিজড়ে এবং সমকামীরা কি একই সমগোত্রীয়? রূপান্তরকামী সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘অন্তহীন অন্তরীণ প্রোষিতভর্তৃকা’ গ্রন্থে বিষয়টা পরিষ্কার করেছেন। তিনি হিজরানী শ্যামলী-মায়ের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন– “এতদিনে মানুষের ধারণা ছিল হিজড়ে বুঝি জন্ম থেকেই হয়। ছোটোবেলাতেই হিজড়ে সন্তান জন্মালে মা-বাবা তাকে হিজড়ে ডেরায় দিয়ে আসে। কেন– এমন গল্প শুনিসনি, হিজড়ে বাচ্ছাকে মা-বাবা আটকে রেখেছিল, পাড়ায় হিজড়েরা তালি দিচ্ছিল, আর সেই তালি শুনে ঘর থেকে বাচ্ছা হিজড়ে তালি দিল। আর সেই তালি শুনে হিজড়েরা বাচ্ছাটাকে নিজেদের সঙ্গে নিয়ে চলে গেল!”
হিজড়া হতে হলে লিকস্ (লিঙ্গ) ছিবড়াতে (কর্তন) হয়। অণ্ডকোশ সমেত পুরুষাঙ্গ কেটে ফেললে তবেই ‘নির্বাণ’ বা প্রকৃত সন্মানিত হিজড়া হওয়া যায়। অবশ্য পুরুষাঙ্গ কর্তন করতেই হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। পুরুষাঙ্গ নিয়ে যে ধুরানি (বেশ্যা বা যৌনকর্মী) হিজড়া বৃত্তি করবে, তাকে হিজড়ারা ‘আকুয়া’ (বিপরীত সাজসজ্জাকামী ও যৌনপরিবর্তনকামী) বলে।
ওরা ঢোল বাজিয়ের দল, ওরা হিজড়া। ওরা নবজাতকের খোঁজে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়, ওরা হিজড়া। ওরা এক শ্রেণির অবাঞ্ছিত, অপাঙক্তেয় মানবগোষ্ঠী, ওরা হিজড়া। ওরা যৌন বিকলাঙ্গ– এক প্রতিবন্ধী মানুষ, ওরা হিজড়া। মনুষ্য সমাজে এক অন্তঃসলিলা প্রবাহ, যাঁরা প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে চলে আসছে সমাজের উন্থানপতন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে, ওরা হিজড়াই। প্রাণীজগতে আমরা চার প্রকারের ‘হিজড়া’ দেখতে পাই।
(১) প্রকৃত হিজড়া (True Hermaphrolite),
(২) পুরুষ অপ্রকৃত হিজড়া (Male Pseudo Hermaphrodite),
(৩) স্ত্রী অপ্রকৃত হিজড়া (Female Pseudo Hermaphrodite) এবং
(৪) ফ্ৰিমার্টিন সিনড্রোম (Freemartin Syndrome)।
প্রকৃত হিজড়াদের ক্ষেত্রে একই দেহে শুক্রাশয় ও ডিম্বাশয়ের অবস্থান লক্ষ করা যায়। পুরুষ অপ্রকৃত হিজড়াদের শরীরের আপাত বাহ্যিক গঠন মেয়েলি হলেও শুক্রাশয় বর্তমান। স্ত্রী অপ্রকৃত হিজড়াদের দৈহিক গঠনের সঙ্গে সুস্থ পুরুষের আপাত সাদৃশ্য থাকলেও এরকম হিজড়ার দেহে ডিম্বাশয় থাকে।
হিজড়াদের মূলত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়– (১) জন্মগত হিজড়ে এবং (২) ছদ্মবেশী হিজড়া।
(১) জন্মগত হিজড়ে : আমরা আমাদের চারপাশে যেসব হিজড়া দেখি তাঁদের অনেকেই জন্মগত যৌন প্রতিবন্ধী। এঁদের যৌন জনন বৈকল্য বা প্রতিবন্ধকতা একরকম নয়। কারোর যৌনাঙ্গ অপুষ্ট বা অপূর্ণাঙ্গ। কারোর-বা শরীরে নারী ও পুরুষ অপরিপূর্ণ উভয় যৌনাঙ্গের অবস্থান লক্ষ করা যায়। এখন প্রশ্ন কেন প্রতিবন্ধকতা?
নারী-পুরুষ লিঙ্গ নির্ধারণ হয় দুই ধরনের আলাদা আলাদা ক্রোমোজোমের উপস্থিতিতে। সাধারণত প্রতি কোশে এক জোড়া ক্রোমোজোম দেখা যায়, যারা বস্তুত লিঙ্গ নির্ধারক। এই ক্রোমোজোমগুলিই হল Sex Chromosome বা যৌন ক্রোমোজোম। যৌন ক্রোমোজোম দুটিকে X এবং Y দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। বাকি ক্রোমোজোমগুলি জীবের অন্যান্য বৈশিষ্ঠ্যের ধারক। এঁরা। Autosome বা অযৌন ক্রোমোজোম। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে মানুষের দেহকোশের ক্রোমোজোমের সংখ্যা ৪৬ বা ২৩ জোড়া। এই ২৩ জোড়া ক্রোমোজোমের মধ্যে এক জোড়া ক্রোমোজোম নির্ধারক। অর্থাৎ বাকি ২২ জোড়া অটোজোম। Y ক্রোমোজোমের আকৃতি ও আয়তনে X ক্রোমোজোমের তুলনায় ক্ষুদ্র। স্ত্রী দেহকোশে দুটি X ক্রোমোজোম থাকে। অপরদিকে, পুরুষ দেহকোশে একটি x এবং একটি Y ক্রোমোজোম থাকে। প্রতিটি কন্যা সন্তান মাতাপিতার কাছ থেকে ২২ জোড়া অযৌন ক্রোমোজোম পেয়ে থাকে। এর মধ্যে মায়ের কাছ থেকে একটি X ক্রমোজোম এবং বাবার কাছ থেকে একটি Y ক্রোমোজোম, অর্থাৎ দুটি XX যৌন ক্রোমোজোম পেয়ে থাকে। অপরদিকে পুত্র সন্তানটি ২২ জোড়া অযৌন ক্রোমোজোমের সঙ্গে মায়ের কাছ থেকে একটি x এবং বাবার কাছ থেকে একটি Y ক্রোমোজোম লাভ করে। এটাই স্বাভাবিক হলেও সবসময় তা হয় না। অনেক সময় যৌন ক্রোমোজোমের ত্রুটির ফলে কোনো সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ সন্তানটি ছেলে না মেয়ে, সেটা বলা নির্দিষ্ট করে বলা যাবে না। তখন সে তৃতীয় সেক্সের দলে পড়ে, অর্থাৎ হিজড়া। ক্রোমোজোম ও বাবডির ত্রুটির হিসাবে হিজড়াদের ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন–
(ক) ক্লাইনেফেলটার সিনড্রোম (Klinefelter Syndrome): এদের স্ফীত স্তন দেখা যায়। এদের শিশ্ন বা পুংলিঙ্গ থাকে বটে, তবে তা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। শুক্রাশয়ও খুব ছোটো হয়। বগল (বাহুমূল) চুল বা কেশ থাকে না। এঁদের তলপেটের নীচে, অর্থাৎ যৌনাঙ্গের চারপাশে চুল কম হয়। মুখে দাড়ি-গোঁফ কম হয়। এঁরা সাধারণত উচ্চতায় লম্বা ধরনের হয়ে থাকে। মানসিক জড়তাও থাকতে পারে। এই সমস্ত ব্যক্তিদের দেহকোশে ২২ জোড়া অটোজোম, ২টি x ক্রোমোজোম এবং একটি Y ক্রোমোজোম— মোট ৪৭টি ক্রোমোজোম থাকে। সাধারণ অবস্থায় পুরুষের শরীরে যৌন ক্রোমোজোম থাকে xY এবং মোট ক্রোমোজোমের সংখ্যা হয় ৪৬টি। অতিরিক্ত স্ত্রী যৌন ক্রোমোজোম, অর্থাৎ X এর উপস্থিতির ফলেই ব্যক্তির শরীরে স্ত্রী-বৈশিষ্ট্য প্রকট হয়।
(খ) XXX পুরুষ (xxY Male) : এঁদের শরীরের গঠন পুরুষদের মতো হলেও এঁরা পুরোপুরি পুরুষ নয়। এরা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি লম্বা হয়। এঁদের বুদ্ধিবৃত্তি কম। এঁদের মধ্যে অনেক সময়েই হিংসাত্মক সমাজবিরোধী আচরণের প্রকাশ ঘটে। পুরুষদের মতো লিঙ্গ থাকে। তবে লিঙ্গ থাকলেও মূত্রছিদ্রটি লিঙ্গের স্বাভাবিক স্থানে থাকে না। এঁদের অণ্ডকোশও স্বাভাবিক স্থানে না। থাকে শরীরের অভ্যন্তরে। এঁদের শরীরে ক্রোমোজোমের সংখ্যা ৪৭। ৪৪ টি অটোজোম এবং ৩ টি যৌন ক্রোমোজোম। যৌন ক্রোমোজোমের মধ্যে একটি x এবং দুটি Y ক্রোমোজোম থাকে।
(গ) XX পুরুষ (xx Male syndrome) : XX-পুরুষদের সঙ্গে ক্লাইনেফেলটার সিনড্রোমের অনেক মিল আছে। এদের অনেকেরই স্তন থাকে। তবে তা কখনোই সুডৌল এবং স্ফীত নয়। শুক্রাশয় থাকে, তবে তা খুবই ক্ষুদ্র। তবে শুক্রাশয় থাকলেও সেখানে শুক্রাণু উৎপন্ন হয় না। পুরুষাঙ্গ আকৃতিতে স্বাভাবিক, অথবা স্বাভাবিকের তুলনায় ছোটোও হতে পারে। লিঙ্গের যে স্থানে মূত্রছিদ্রটি থাকার কথা সেখানে থাকে না। XX পুরুষরা উচ্চতায় বেঁটে প্রকৃতির হয়। এই ধরনের XX পুরুষের শরীরে ক্রোমোজোমের মোট সংখ্যা ৪৮। অটোজোম ৪৬ টি এবং দুটি সেক্স ক্রোমোজোম থাকে। XX সেক্স ক্রোমোজোমের উপস্থিতি থাকলেও ক্রোমোজোমের গঠনের অস্বাভাবিকতার জন্য এঁরা পরিপূর্ণ নারী হয়ে উঠতে পারে না। বিভিন্ন রকম পুরুষালি ভাব প্রকট হয়।
(ঘ) টার্নার সিনড্রোম (Turner Syndrome) : এঁদের ক্রোমোজোমের গঠন ক্লাইনেফেলটার সিনড্রোম ও XX-পুরুষ হিজড়াদের অনুরূপ নয়। আপাতদৃষ্টিতে এঁদের নারী মনে হলেও এরা কিন্তু পুরোপুরি নারী নন। কারণ এদের প্রধান যৌনাঙ্গ এবং অন্যান্য গৌণ যৌনাঙ্গ ত্রুটিযুক্ত। এদের যৌনাঙ্গের সঙ্গে নারীর যৌনাঙ্গের আপাত সাদৃশ্য থাকে। যোনিকেশ খুবই কম দেখা যায়। ডিম্বাশয় থাকে না এবং অপূর্ণাঙ্গ ফেলোপিয়ান টিউব ও জরায়ুর গঠন। এর ফলে রজঃস্বলা বা পিরিয়ড হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। এদের বুকের ছাতি পুরুষদের মতো প্রশস্ত। তবে এঁদের প্রশস্ত ছাতিতে কৈশোর থেকে স্তনগ্রন্থির প্রকাশ ঘটে। এঁরা অস্বাভাবিক খর্বাকৃতি হয়। গায়ের চামড়া টানলে অনেকটা ঝুলে পড়ে। হাত-পায়ের অত্যন্ত খসখসে হয়। বৌদ্ধিক ক্ষমতা সাধারণের চাইতে কম। এঁদের কোশের ক্রোমোজোমের সংখ্যা ৪৫ (অটোজোম ৪৪ + x)। বার্বোডি থাকে না। ক্রোমোজোমের এই অস্বাভাবিকতার জন্যেই এঁদের যৌনাঙ্গ ইত্যাদি ত্রুটিযুক্ত হয়। Y ক্রোমোজোমের অনুপস্থিতি যেমন শরীরে পুরুষালি ভাব প্রকাশের অন্তরায় হয়ে শরীরকে নারীসুলভ করে তোলে, ঠিক তেমনই বার্বোডি না-থাকায় নারী শরীরের স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে না। দেহের গঠন আংশিক পুরুষের মতো হয়ে থাকে।
(ঙ) মিশ্র যৌনগ্রন্থির বিকৃতি (Mixed Gonadal Dysgenesis) : আপাতদৃষ্টিতে এঁদের পুরুষ বলেই মনে হয়। গোঁফ-দাড়িও হয়। শুক্রাশয় থাকে, তবে তা থাকে শরীরের অভ্যন্তরে। এই প্রকার হিজড়াদের শুক্রাশয়ের বিভিন্ন প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যই পরিণত শুক্রাণুর জন্ম হয় না। এদের শিশ্ন বা লিঙ্গ বর্তমান থাকে। মূত্রছিদ্র লিঙ্গের স্বাভাবিক স্থানেই থাকে। ব্যতিক্রম যেটা, সেটা হল লিঙ্গ থাকা সত্ত্বেও এদের শরীরে যোনি অর্থাৎ স্ত্রীযোনি, জরায়ু এবং ফেলোপিয়ান টিউব থাকে। কৈশোরের এদের শুক্রাশয় থেকে এন্ড্রোজেন নিঃসৃত হয়, ফলে শরীরে পুরুষালি ভাব বেশ প্রকট হয়ে ওঠে। প্রধানত ক্রোমোজোমের অস্বাভাবিকতা, অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডের নানারকম ত্রুটি এবং জননকোশের উৎপত্তি স্থানের নানা সূক্ষ্ম জটিলতার ফলেই এমন যৌনবিকলাঙ্গ মানুষের জন্ম হয়। এইসব মানুষদের দেহকোশে ক্রোমোজোমের সংখ্যা সাধারণত ৪৬ (৪৫ + X) হয়। অবশ্য অনেক সময়েই ৪৭ (৪৫ + XY)ও দেখা যায়।
বস্তুত হিজড়াদের দলে জন্মগত যৌন-প্রতিবন্ধীর সংখ্যা খুবই নগণ্য। সামান্য কিছু ব্যতীত প্রায় সকলেই ছদ্মবেশী হিজড়া। তবে শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে এঁরা এত বেশি অসুস্থ যে খোশমেজাজে নেচে-গেয়ে হিজড়াদের দলে থেকে এঁদের জীবন কাটিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। নানাবিধ শারীরিক পীড়ায় জর্জরিত এঁরা। আর পাঁচটা অসুস্থ-পঙ্গু মানুষের মতো এরা সংসারের বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। তাই সম্প্রদায়ভুক্ত হিজড়াদের দলে এঁদের ঠাঁই হয় না। এঁদের কাছেও এরা ঝঞ্ঝাট। অন্যভাবে বললে এরা ‘অপ্রকৃত হিজড়া’। প্রসঙ্গত জানাই, যৌন-প্রতিবন্ধী যাঁরা, তাঁদেরকে ‘প্রকৃত হিজড়া’ বলা হয়। প্রকৃত হিজড়াদের সকলকেই পুরোপুরি সারিয়ে তোলা সম্ভব না-হলেও চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে অনেকেই ত্রুটিমুক্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে। যদিও ক্রোমোজোমের অস্বাভাবিকতা থাকলে তাঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনা যায় না ঠিকই, কিন্তু হাইপোস্পিডিয়াস থাকলে তাঁকে সার্জারির সাহায্যে ভালো করে তোলা সম্ভব হয়েছে। টানার্স সিনড্রোমে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও অস্ত্রোপচার সম্ভব হচ্ছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আগামীদিনে জন্মগত হিজড়ে অনেক কমে যাবে বলে অনেকে মনে করেন।
(২) ছদ্মবেশী হিজড়া : ছদ্মবেশী হিজড়াদের চারভাগে ভাগ করলে আলোচনার সুবিধা হবে। যেমন–
(ক) আকুয়া : হিজড়া দলে এক ধরনের পুরুষ থাকে যাঁরা মেয়ে সাজতে চায়, মেয়ে হতে চায়। মেয়ে হিসাবে নিজেকে জাহির করার মধ্যে এঁরা অসম্ভব রকম মানসিক পরিতৃপ্তি বোধ করে। এঁরা পুরুষ হলেও নারী-বেশ ধারণ করতে পছন্দ করে। স্রেফ এক বিশেষ মানসিক তাড়নায় এঁরা মেয়ে সেজে থাকতে চায়। সদ্য শৈশব পেরিয়ে আসা কিশোরদের মধ্যে এরকম ভাব লক্ষ করা যায়। তবে পরিণত বয়সেও কোনো পুরুষের মধ্যেও এ ধরনের মানসিকতা সৃষ্টি হতে পারে। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় এঁদের মানসিকতাকে Transexualism বা লিঙ্গরূপান্তরকামিতা বা যৌন পরিবর্তনকামিতা বলে। নিজেকে পুরোপুরি পালটে মহিলা হিসাবে পরিচিত হতে চায়। যৌন পরিবর্তনকামী মানুষরা নারীত্বের স্বাদ পেতে চায়। পুরুষদের এঁরা প্রেমিকা ভাবে। কৃষ্ণনগর উইমেন্স কলেজের সদ্য নিযুক্ত মানবী বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন আগে পর্যন্তও ‘আকুয়া’ সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হিসাবে পরিচিত ছিলেন। আজ বিজ্ঞানের কল্যাণে ‘পুরুষ’ সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে নারী হিসাবে মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুনর্জন্ম হয়েছে।
এই আকুয়ারা সমবয়সিকে স্রেফ বন্ধু হিসাবে পেতে চায়, যৌনসঙ্গী হিসাবে নয়। কিন্তু পুরুষ হয়েও মেয়েলি স্বভাব ও আচরণের জন্য মেয়েরা তাঁদের মেয়ে হিসাবে মেনে নিতে পারে না। মেয়েলি ভাবের জন্য এঁরা যেমন মেয়েদের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হয়, তেমনি পুরুষদের কাছ থেকেও প্রত্যাখ্যাত হয়। ফলে এদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ ও অন্তর্মুখীনতা দেখা যায়। দারিদ্র্য, সাংসারিক ও পারিপার্শ্বিক চাপে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠা আকুয়ারা একটা সময় হিজড়াদের দলে এসে ভিড়ে যায়। সবার ভাগ্যে তো আর মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ঘর ও বর জোটে না!
(খ) জেনানা : জেনানা হল নারীর সাজে সজ্জিত কোনো পুরুষ। তবে এঁদের আকুয়া বলা যাবে না। কারণ জেনানারা কোনো বিশেষ মানসিকতার দ্বারা আক্রান্ত নয়। নারী বেশ ধারণের মধ্য দিয়ে এঁরা কোনো সুখ উপলব্ধি করে না। যৌন-প্রতিবন্ধী হিসাবে পরিচিত হয়ে এঁরা সমাজের কাছ থেকে সর্বপ্রকার বাড়তি সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে চায়। কম খেটে অসদুপায়ে বেশি রোজগারের আশায় জেনানা হিজড়াদের এই ধরনের নারীবেশ ধারণ। হিজড়ার জগতে জেনানাদের দাপটই সবচেয়ে জেনানারা আবার দু-ধরনের হয়। যেমন —
(অ) যৌনক্ষমতাহীন জেনানা : হিজড়া দলের এইসব জেনানারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমাজের এক্কেবারে পিছিয়ে-পড়া শ্রেণির মানুষ। অস্বাস্থ্যকর ঝুপড়ি বস্তি এলাকা থেকেই এইসব হিজড়ারা সংগৃহীত হয়। এদের কেউ কেউ অনাথ। এঁরা স্বেচ্ছায় হিজড়াদের দলে চলে আসে। দারিদ্র্য, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা এবং অল্প পরিশ্রমে রোজগারের হাতছানি যৌনক্ষমতাহীন ব্যক্তিদের হিজড়াদের ডেরায় ভিড়ে যায়।
(আ) যৌনক্ষমতাসম্পন্ন জেনানা : এঁরা শরীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে পরিপূর্ণ সুস্থ পুরুষ-মানুষ। এঁরা ধান্দাবাজ, ধুরন্ধর। এঁদের অনেকেরই স্ত্রী-সন্তান পরিবার থাকে। কোনো জেনানা যদি হিজড়েদের দলের প্রধান হয় তাহলে তাঁর পক্ষে তাঁর পরিবারের সঙ্গে থাকা সম্ভব হয় না। দল পরিচালনার জন্যে তাঁকে হিজড়া-মহল্লাতেই থাকতে হয়। তাই বলে পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নষ্ট হয় না। সেই কারণেই এদেরকে রোজ ভোর হতে না-হতেই ছুটতে হয় হিজড়েদের দুনিয়াতে।
(গ) ছিবড়ি : শুধু পুরুষরাই নয়, হিজড়াদের দলে কিছু মহিলাদেরও দেখা যায়। এইসব হিজড়াদের ছিবড়ি বলা হয়। এঁরা যৌনাঙ্গের ত্রুটিযুক্ত মহিলা নয়, সুস্থ সবল মানুষ এঁরা। নিতান্তই অর্থনৈতিক কারণেই এঁরা হিজড়ের দলে এসে যোগ দেয়। চরমতম আর্থিক সংকটের মধ্যেই দিন গুজরান করে। রুটিরুজির ধান্দায় এঁরা হিজড়াদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। হিজড়াদের সঙ্গে থাকার কারণে হিজড়াদের আদব-কায়দাও শিখে নেয়। রপ্ত করে নেয় হিজড়া সমাজের রীতিনীতি। এঁরা বেশিরভাই বিবাহিতা এবং স্বামী পরিত্যক্তা হন।
(ঘ) ছিন্নি : যে সমস্ত পুরুষ মানুষ লিঙ্গ কর্তন করে ‘খোজা হয়, তাঁদেরকেই ‘ছিন্নি’ বলে। হিজড়াদের গরিষ্ঠাংশই ছিন্নি। আকুয়া থেকে অনেকে হিজরাই স্বেচ্ছায় ছিন্নিতে রূপান্তরিত হয়। যৌন পরির্তনকামী হিজড়ারা নিজেদের পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলে। শরীর থেকে পুরুষাঙ্গ কর্তন করে পরিপূর্ণ নারী হওয়ার স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে। আধুনিক বা অগ্রসর দেশগুলিতে অত্যাধুনিক প্ল্যাস্টিক সার্জারি করে যৌন পরিবর্তনকামীরা তাঁদের লিঙ্গ পরিবর্তন করার সুযোগ পেতে পারে। এই জাতীয় অস্ত্রোপচার অত্যন্ত ব্যয়বহুল, তাই অনেকেরই এই স্বপ্ন অধুরাই থেকে যায়। তবে যাঁরা অসম্ভব রকমের মানসিক টানাপোড়েনকে উপেক্ষা করতে পারেন না, তাঁরা হাতুড়ে চিকিৎসক দিয়ে লিঙ্গ কর্তন করিয়ে নেয়। অবশ্য যৌন পরিবর্তনকামী আকুয়ারা ছাড়াও যৌনক্ষমতাহীন জেনানারাও অনেক সময় তাঁদের লিঙ্গ কর্তন করায়। এছাড়া দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দালাল মারফত পুরুষ-শিশু, কিশোর এবং যুবকদের হিজড়াদের গোষ্ঠীপতিরা সংগ্রহ করে। এরপর ওদের লিঙ্গ কর্তন খোজা করে ‘পাকা হিজড়া’ বানিয়ে তাঁদের বিভিন্ন রকম রোজগারের কাজে নামানো হয়।
খোজার কথা যখন উঠলই তখন আমরা জেনে নিতে পারি খোজার ইতিহাস। কীভাবে খোজা’ (ক্যাসট্রেশন) করা হয় তাও জানব। খোজাদের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় মানুষের হাতে গড়া খোজাদের আবির্ভাব হয়েছিল মেসোপটেমিয়ায়। খোজা প্রাচীন ও মধ্যযুগে রাজকীয় হারেমে বা জেনানামহলে কর্মী ও কর্মকর্তা হিসাবে নিযুক্ত খোজাকৃত পুরুষ। বিশেষ উদ্দেশ্যে পুরুষদের খোজা করার প্রথা খ্রিস্টপূর্ব আট শতকের গোড়ার দিকেও প্রচলিত ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগে খোজারা রাজকীয় হারেমের ভৃত্য বা প্রহরী হিসাবে, খেতাবধারী বা বৃত্তিভোগী রানি এবং সরকারের যোদ্ধা ও মন্ত্রীদের পরামর্শদাতা হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। এ প্রথা বা ব্যবস্থাটি ভারতে প্রবর্তিত হয় সম্ভবত সুলতানি আমলের গোড়ার দিকে। খোজাদের প্রধানত সুলতানদের প্রাসাদে হারেম প্রহরার জন্য নিযুক্ত করা হলেও চিনা খোজাদের মতো সুলতানি আমলের খোজারা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক ভূমিকা পালন করে। সুলতান আলাউদ্দিন খলজির (১২৯৬-১৩১৬) অন্যতম বিখ্যাত সেনাপতি ও ওয়াজির মালিক কাফুর একজন খোজা ছিলেন। দিল্লির খোজাদের মতো বাংলার অভিজাতবর্গের খোজারাও প্রশাসনে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে। বাংলায় হাবশি শাসনামলে (১৪৮৭-১৪৯৩) বস্তত শাসকদের ক্ষমতার উত্থান-পতনে তাদের অংশগ্রহণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। শাহজাদা ওরফে বারবক নামে এক খোজা ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দে বাংলার মসনদ দখল করেন। পণ্ডিতদের বিশ্বাস, হাবসি সুলতান শামসউদ্দিন মুজাফফর শাহ (১৪৯০-১৪৯৩) খোজা ছিলেন। সমসাময়িক বাংলায় পর্তুগিজ পরিব্রাজক দুয়ার্তে বারবোসার বিবরণ অনুসারে বাংলার শাসক ও অভিজাতবর্গের হারেমগুলিতে দেশীয় ও বিদেশি বংশোদ্ভূত খোজারা প্রহরায় নিয়োজিত থাকত। কথিত আছে, নওয়াব শুজাউদ্দিন খানের (১৭১৭-১৭৩৯) হারেম প্রহরায় নিয়োজিত ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে সংগৃহীত খোজারা।
ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক নানা গবেষণা থেকে জানা যায় যে, বহুবিবাহ, উপপত্নী (বাঁদি) ও হারেম ব্যবস্থা গড়ে ওঠার কারণে খোজা ব্যবস্থারও উদ্ভব ঘটে। হারেমের নারীদের উপর নজর রাখার জন্য খোজাকৃত পুরুষ প্রহরী নিয়োগ করা হত। পুরুষদের খোজা করে দেওয়া হত এই কারণে যে, যাতে এই পুরুষ-প্রহরীরা হারেমের নারীদের সঙ্গে যৌনমিলন না করতে পারে। সাধারণত রণাঙ্গণে বন্দি তরুণ সৈনিকদের খোজা করা হত। এছাড়া দাস-বিক্রেতারা সাধারণত দাস বাজার থেকে ক্রয় করে স্বাস্থ্যবান ও তরুণ বালকদেরও খোজা করত। এরপর শাসক ও অভিজাতবর্গের হারেমে বিক্রি করে দিত। ভারতের প্রাচীন শাসকরা তাঁদের হারেম পাহারা দেওয়ার জন্য হিজড়াদের নিয়োগ করতেন, কখনো তাঁরা খোজা করা কোনো পুরুষকে নিয়োগ করতেন না। অতএব খোজা প্রথা এদেশে প্রবর্তিত হয় বিদেশিদের দ্বারাই।
সভ্যতার একেবারে গোড়ার দিকে, অর্থাৎ খ্রিস্টপূর্ব ৮১১ থেকে ৮০৮ অব্দের আসিবিয়ার রানিমাতা সামুরামাত নিজ হাতে তার এক ক্রীতদাসকে ‘খোজা’ করেছিলেন। একটি উপকথায় তাঁকে সেমিরা মিস বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আসিবিয়ার রানিমাতা কেন তাঁর ক্রীতদাসকে ‘খোজা’ করেছিলেন ইতিহাসে তার বিবরণ না-থাকলেও অনেক গবেষক মনে করেন রানির বিকৃত যৌন-লালসা নিবৃত্ত করার জন্য হতভাগ্য ক্রীতদাসকে বিকলাঙ্গ করা হয়েছিল।
এরপর বিভিন্ন দেশে ‘খোজা’ করা হয়েছে। আর এই নিষ্ঠুরতা সংঘটিত হয়েছে শাসক, অভিজাত শ্রেনি এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিদের মহলেও। শুধু যে রাজা-বাদশা বা অভিজাত শ্রেণির মহলে খোজা তৈরি হত তা কিন্তু নয়, ধর্মীয় কারণে অনেকেই খোজাকরণ বরণ করেছে, ইতিহাসে এর প্রমাণও আছে। ওল্ড টেস্টামেন্টে খোজার উল্লেখ আছে। ম্যাথুর প্রবচনে আছে— ‘একদল পুরুষত্বহীন মানুষ আছে যারা মাতৃগর্ভ থেকেই অসম্পূর্ণ অবস্থাতে ভূমিষ্ট হয়েছে। আর একদল আছে যাদের অন্য মানুষ খোজা করেছে। তৃতীয় দলের খোজা যাঁরা তাঁরা স্বর্গের কামনায় স্বেচ্ছায় পুরুষহীন হয়েছে। এই কথার পরিপ্রেক্ষিতেই বোধহয় একজন খ্রিস্টান ধর্মযাজক ঘোষণা করেছিলেন— একমাত্র কামনাশূন্য খোজার কাছেই স্বর্গের দুয়ার খোলা রয়েছে। কামনা-বাসনা শূন্য হওয়ার জন্য অনেক ধর্মপ্রচারক খোজাদের স্বপক্ষে তাঁদের অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কামনাশূন্য সাধনা করার জন্য বিগত খ্রিস্টান সাধু ওরিজেন তার পুরুষত্ব বিসর্জন দিয়েছিলেন। ১৭৭২ সালে রাশিয়ায় একটি গোপন ধর্মীয় গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটেছিল, যাঁরা স্বেচ্ছায় খোজাকরণ বরণ করে নিতেন। এঁদের বিশ্বাস ছিল মানুষের দেহে আদম এবং ইড থেকে যে নিষিদ্ধ ফল যৌন-তাড়না করে বেড়াচ্ছে, খোজাকরণের মাধ্যমে তার অবসান ঘটানো সম্ভব। মানব এবং মানবীর জনক এবং জননী হওয়ার যোগ্যতা এই নিষিদ্ধ অদৃশ্য ফল থেকেই আসে, আর লিঙ্গ ও যোনির ব্যবহারে আর একটি মাত্র সন্তানের জন্ম হয়। এ কারণেই রাশিয়ার ওই গোপন সংগঠনের পুরুষ সদস্যরা স্বেচ্ছায় খোজা এবং নারীরা তাঁদের স্তন কেটে কামনাশূন্য হতে চেয়েছিল।
খ্রিস্টানদের মধ্যে স্বর্গ প্রাপ্তির আশায় শুধু খোজাকরণ বরণ করত, তা কিন্তু নয়। গির্জায় প্রার্থনা সংগীত গাওয়ার জন্য খোজাদের কদর করা হত। সিসটান চ্যাপেলে প্রার্থনা সংগীত গাওয়ার জন্য স্বয়ং পোপ তাঁদের আহ্বান করতেন। খোজাদের আহ্বান করার পিছনে যুক্তি ছিল খোজাদের কণ্ঠস্বর সমান তেজি, সমান গভীর এবং সমান নিখাদ। খ্রিস্ট সম্প্রদায় এই সংগীত আগ্রহভরে শ্রবণ করত, তাঁদের বিশ্বাস ছিল ঈশ্বরকে মুগ্ধ করার জন্য খোজা কণ্ঠের সংগীত অবশ্যই গীত হওয়া প্রয়োজন। এই ধারণা থেকে ইতালির অনেক বিখ্যাত গায়ক স্বেচ্ছায় খোজা হয়ে গিয়েছিলেন।
এখানেই শেষ নয়, হারেমের প্রহরী হিসাবেও খোজারা নির্ভরযোগ্য ছিল। খোজাদের এই বিশ্বস্ততা প্রথম লক্ষ করেন সাইরাস। তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৫৩৮ অব্দে ব্যাবিলন দখল করার পর আবিষ্কার করলেন খোজাদের মতো নির্ভরযোগ্য পুরুষ সত্যিই দুর্লভ। তার এই আবিষ্কারের পিছনে যুক্তি ছিল খোজাদের যেহেতু কোনো সংসার নেই, তাই যে তাকে প্রতিপালন করবে খোজারা সুখ-দুঃখে তারই পাশে থাকবে। সাইরাস এও লক্ষ করেছিলেন যে, খোজারা পুরুষত্বহীন বলে কিন্তু তারা হীনবল নয়। সাইরাস এই বিশ্বাস থেকেই রাজ অন্তঃপুরে খোজা প্রহরী নিয়োগ করেছিলেন। এরপর বিভিন্ন দেশের হারেমে খোজা প্রহরীদের নিয়োগের হিড়িক পড়ে যায়।
হেরোডোটাসের বর্ণনা থেকে জানা যায়, পারস্যের মানুষরা আইনিয়ানদের দলে দলে বন্দি করে তাঁদের পুরুষত্বের বিনাশ করত এবং এঁদের সুন্দর পোশাক-আশাক পরিয়ে বিভিন্ন দেশের রাজাদের কাছে বিক্রি করে দিত। হেরোডেটাস বলেছেন– সম্রাট জারেজেসের প্রিয় খোজা-পুরুষ ছিলেন হারমোটিয়াস নামে এক ব্যক্তি। শিশুকালে তাঁকে অপহরণ করে দাস বিক্রেতাদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়। এরপর দাস-বিক্রেতারা ভালো দাম পেয়ে তাঁকে পানিওনিয়াস নামে এক ধনী ব্যক্তির কাছে বিক্রি করে দেয়। সে ছিল খোজাকরণে দক্ষ। পানিওনিয়াসই বালক হারমোটিয়াসকে খোজা করে বাজারে নিয়ে আসে। এরপর আর-এক ব্যবসায়ীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। এইভাবে হাতবদল হতে হতে হারমোটিয়াস একদিন জারকজেসের দরবারে পৌঁছে যায়।
পারসিকরাই মুসলিম শাসিত রাজ্যে প্রথম খোজার আমদানি করেছিল। তুর্কিরা তো খোজার খোঁজই রাখতেন না। অবশ্য পঞ্চদশ শতাব্দীতে খোজার সন্ধান পান তুর্কি শাসকরা। এই আশ্চর্য বিশ্বস্ত এবং শক্তিমান না-নারী না-পুরুষ প্রাণীটি পেয়ে তুর্কিদের মধ্যে এই চেতনার উদয় হল যে, ইচ্ছে করলে তা তাঁরা নিজেরাই খোজা তৈরি করতে পারে।
তুর্কি সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগে অসংখ্য যুদ্ধবন্দির মাঝখান থেকে রূপবান এবং শক্তিমান পুরুষদের বেছে বেছে খোজা তৈরির মহরত শুরু করেন সুলতান প্রথম মাহমুদ এবং দ্বিতীয় মুরাদ। খোজাদের প্রথমদিকে বাদশাহ বা সুলতানের মহিষী এবং রক্ষিতাদের পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হলেও পরবর্তী সময় সুলতানের হেঁসেল থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজে তাঁদের নিয়োগ করা হত।
১৮৩৬ সালে মুর্শিদাবাদের এক প্রাসাদে ৬৩ জন খোজার অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছিল। এই খোজারা শুধু আজ্ঞাবাহী ভৃত্য হিসাবে নিয়োজিত ছিল না, তাঁরা সম্রাট এবং নবাবের প্রিয়পাত্র হিসাবে কোনো কোনো সময় শাসনকার্যে প্রভাব বিস্তার করত। ইতিহাসে এ রকম একটি ঘটনার কথা জানা যায়, ঘটনাটি ঘটেছিল তুর্কি হারেমে। তুর্কিমহলের খোজা প্রধানকে বলা হত কিসলার আগা। কিসলার আগা উপাধিধারী খোজা শুধু মহলের কুমারীদের প্রধান রক্ষী হিসাবে নিয়োজিত হত। সে নিজে দাস হলে তার অধীনে থাকত চারশো গোলাম-বাঁদি। তার নামে ঘোড়াশালে আলাদা করে রেখে দেয়া হত তিনশো ঘোড়া। পুরুষত্বহীন একজন মানুষের এই বিপুল ক্ষমতা একজন খোজার শুধু অটোমান সাম্রাজ্যেই দেখা যায়নি, ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায় মোগল আমলে অযোধ্যার একজন জনপ্রিয় আঞ্চলিক শাসক ছিল খোজা। স্পষ্টত মুসলিম বিশ্বে প্রেরিত কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসদের সব বা অতি উচ্চ অংশকে খোজা করা হয়েছিল, যার কারণে এসব অঞ্চলে তারা উল্লেখযোগ্য বংশধর (ডায়াসপোরা’) রেখে যেতে ব্যর্থ হয়। ইসলামি ক্রীতদাসত্বের নিদারুণ লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়া ইউরোপীয়, ভারতীয়, মধ্য-এশীয় ও মধ্যপ্রাচ্যের লক্ষ লক্ষ বিধর্মীর ভাগ্যও অনেকটা একইরকম ছিল। ১২৮০-র দশকে মার্কোপোলো ও ১৫০০-র দশকে দুয়ার্ত বার্বোসা স্বচক্ষে ভারতে বিপুল সংখ্যায় খোজাকরণ প্রত্যক্ষ করেছেন। একই প্রক্রিয়া চলে সম্রাট আকবর (মৃত্যু ১৬০৫), জাহাঙ্গীর (মৃত্যু ১৬২৮) ও আওরঙ্গজেবের (মৃত্যু ১৭০৭) শাসনামলে। সুতরাং, ভারতে গোটা মুসলিম শাসনামলে খোজাকরণ ছিল একটা প্রচলিত নিয়ম। সম্ভবত এটা ইতিপূর্বে উল্লেখিত ভারতের জনসংখ্যা ১০০০ খ্রিস্টাব্দে প্রায় ২০ কোটি থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে ১৭ কোটিতে হ্রাসকরণে একটা বড়ো অবদান রেখেছিল।
খোজাদের মধ্যে বুদ্ধিমান এবং স্মৃতিশক্তিধর হিসাবে যাঁদের পাওয়া যেত সুলতান এবং সম্রাটেরা তাঁদের রাজকার্যে নিয়োজিত করতেন। তবে বুদ্ধিমান খোজার সংখ্যা ছিল খুবই কম। খোজাদের নিয়ে গবেষণায় দেখা গেছে অধিকাংশ খোজাই বদমেজাজি, বালসুলভ, প্রতিশোধপরায়ণ, নিষ্ঠুর এবং উদ্ধত। অবশ্য এর বিপরীত স্বভাবের খোজাও রয়েছে। এঁরা সরল, নিরীহ, আমোদপ্রিয় উদার। অবশ্য খোজাদের মেজাজ মর্জি এই বৈপরীত্যের কারণ তাঁদের খোজাকরণের বয়সের উপর নির্ভর করত। কম বয়সে খোজা করার পর ওই খোজা কারও উপর ক্রোধান্বিত হলে এবং সুযোগ পেলে তাঁকে হত্যা করতেও দ্বিধা করত না।
জে. রিচার্ড লিখিত ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায়, সাধারণভাবে খোজা বা পুরোপুরি অক্ষম এই কথাটা ব্যাপকভাবে প্রচলিত থাকলেও খোজারা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যৌন-অক্ষম নয়। রিচার্ড একজন বিবাহিত খোজার স্ত্রীর সংগে আলাপের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, স্ত্রীলোকটির কথায় মনে হচ্ছিল ওরা পুরোপুরি তৃপ্ত এবং সুখী। চিয়েন লুঙের আমলে একটি ঘটনা থেকে জানা যায়, পিকিংয়ের হারেমের এক খোজা পুরোহিতের কাছে ঔদ্ধত্ব প্রকাশ করে বলেছিল, খোজার উপর পুরোহিতের কোনো এক্তিয়ার নেই। পুরোহিত খোজাকে হেকিমের কাছে নিয়ে গেলেন। পরীক্ষা করে দেখা গেল তাঁর পৌরুষত্ব ফিরে এসেছে। আসলে সে ছিল এক নকল খোজা।
প্রাচীন চিনে শাসক বা রাজারা রক্ষিতা রাখার ব্যাপারে অনেকটা এগিয়ে ছিল। বিস্তৃত চিনের অবস্থা ছিল যে, যাঁর যত বেশি রক্ষিত নারী আছে সমাজে তাঁর স্ট্যাটাস তত উঁচুতে। সম্রাটদের ক্ষেত্রেও রক্ষিতা রাখার প্রচলন ছিল। কোনো কোনো সম্রাটের হারেমে হাজার হাজার রক্ষিতা থাকত। মিঙ রাজবংশ এই দিক থেকে বিখ্যাত। মিঙ শাসনামলে তাঁদের হারেমে ২০ হাজার ছিল। যেন পালিয়ে না যায় বা ভিতরে কোনো ঝামেলা না করে সে কারণে পাহারাদার রাখা হত। তবে পাহারাদাররা অবশ্যই পুরুষ ছিল। পাছে রক্ষিতাদের সঙ্গে যৌন সম্পর্কগড়ে তোলে, তাই সেইসব যৌনক্ষমতা নষ্ট করে দেওয়া হত খোজাকরণের মাধ্যমে। ইংরেজি Eunuch শব্দের প্রতিশব্দ হল খোজা। ইউনাক শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ Eunoukhos থেকে, যার অর্থ শয়নকক্ষের পাহারাদার।
খোজাকরণ মূলত তিনটি পদ্ধতিতে করা হত। যেমন– (১) পুরুষাঙ্গ বা লিঙ্গ সমূলে কর্তন করা, (২) অণ্ডকোশ বা শুক্রথলি কর্তন করা এবং (৩) পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোশ উভয়ই কর্তন করা।
প্রাচীন চিনে এই তিনপ্রকার কর্তনই প্রচলন ছিল। এই প্রক্রিয়ায় খুব ধারালো ছুরির সাহায্যে পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোশ উভয়ই কেটে ফেলা হত। চিনে খ্রিস্টপূর্ব ১৬০০ অব্দ থেকে শুরু করে পরবর্তী কয়েক হাজার বছর পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল। তবে এই প্রক্রিয়ায় ঝুঁকি অনেক বেশি। এই প্রক্রিয়ায় অসংখ্য পুরুষের মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যুহার কমানোর জন্য অবশেষে পুরুষাঙ্গ রেখে শুক্রথলি কেটে খোজা বানানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়। পরবর্তীতে চিনের খোজাকরণ প্রক্রিয়া আরও উন্নত করা হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুহারও কমতে শুরু করে। এই কাজে এতটাই পারদর্শী হয়ে ওঠে যে মৃত্যুহার শূন্য হয়ে যায়। প্রাচীন চৈনিক সাম্রাজ্যে খোজাকরণের কাজটি করা হত মূল প্রাসাদের বাইরে বিচ্ছিন্ন কোনো জায়গায়। রাজপ্রাসাদের চারদিকে দেয়াল-ঘেরা সীমানা থাকত। এই সীমানার কোনো স্থানে ব্যবহৃত হয় না এমন একটি পাহারাকক্ষ ব্যবহার করা হত খোজাকরণের অপারেশনের কক্ষ হিসাবে।
কীভাবে খোজা করা হত? প্রথমে ব্যক্তিটিকে ওই কক্ষে নিয়ে গিয়ে একটি কাঠের পাটাতনে শুইয়ে দেওয়া হত। এরপর হালকা গরম জলে যৌনাঙ্গ ও যৌনাঙ্গের আশেপাশে ধুয়ে নেওয়া হত। তারপর ওই স্থানটুকু অবশ করতে পারে এমন উপাদানের প্রলেপ দিয়ে যৌনাঙ্গকে অবশ করে নেওয়া হত। তখনকার সময়ে অবশকারী উপাদান হিসাবে প্রচণ্ড ঝালযুক্ত লঙ্কা বাটা ব্যবহার করা হত। যিনি খোজাকর্মটি করবেন তিনি হচ্ছেন অপারেশন প্রধান। প্রধানের পাশাপাশি কয়েকজনের সহকারীও থাকত। পুরুষাঙ্গ অবশ করার পর সহযোগীরা পুরুষটিকে কাঠের পাটাতনের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে ফেলত। এরপর দুজন সহকারী তাঁর দুই পা ফাঁক করে ধরে থাকত, যেন পুরুষাঙ্গ কর্তনের সময় পায়ের দ্বারা কোনো বাধার সৃষ্টি না হয়। দুইজন সহকারী দুই পা শক্ত করে ধরে রাখতই, তার উপর আরও দুজন কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে একজন হাতদুটি বেঁধে চেপে ধরে রাখত। কর্তক ব্যক্তি সুবিধামতো পুরুষটির দুই পায়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে অণ্ডকোশ ও পুরুষাঙ্গ একসঙ্গে মুঠোর ভিতর ধরে নিত। মুঠোর মধ্যে শায়িত পুরুষটির কাছ থেকে সম্মতি (অসম্মতির কোনো প্রশ্নই নেই, এটা ছিল প্রোটোকল) নেওয়া হত যে, তিনি স্বেচ্ছায় খোজাকরণ করতে দিচ্ছেন। সম্মতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখের পলকেই ধারালো ছুরি দিয়ে একসঙ্গে কর্তন করে দিত পুরুষাঙ্গ ও অণ্ডকোশ। পুরুষটি তীব্র যন্ত্রণায় আর্ত চিৎকার করে উঠত। কর্তন প্রক্রিয়া শেষ হলে মূত্রনালিতে একটি প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হত, যাতে মূত্রত্যাগ করতে পারে। নলটি ছিল অনেকটা আজকের যুগের স্যালাইনের পাইপের মতো। আজ রাজা-সম্রাটদের হারেমে হাজার হাজার নারী রাখার প্রথা বিলুপ্ত হয়েছে। পাশাপাশি বিলুপ্ত হয়েছে খোজাকরণের মতো চরম নিষ্ঠুর এটি রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। তবে রাজার আমল না থাকলেও হিজড়াসমাজে আজও খোজাকরণ হয়ে থাকে।
রাজা-সুলতান-বাদশাহদের হারেমের জন্য খোজার প্রয়োজনীয়তার যে কারণগুলি পাওয়া যায়, তা হল –
(১) হারেম ও অন্দরমহলে থাকত হাজার হাজার পত্নী ও উপপত্নী, স্বামীর সঙ্গে যৌনমিলনের সুযোগ কম পেত। ফলে সেসব নারীর অধিকাংশের যৌনাকাঙ্ক্ষা অতৃপ্ত থেকে যেত। সেই সঙ্গে তাঁদের স্বামীদের বহু নারীর সঙ্গে যৌনসংসর্গে লিপ্ত থাকাটা মেনে নিতে বাধ্য হত। এর ফলে ঈর্ষা ও আক্রোশের জন্ম নিত। এ অবস্থায় হারেমে বা অন্দরমহলে পুরুষ ক্রীতদাস রাখা স্বামীর জন্য ছিল উদ্বেগের বিষয়। কারণ যৌন অতৃপ্ত ও ঈর্ষাপূর্ণ ওসব নারীরা পুরুষ ক্রীতদাসদের সঙ্গে সহজেই যৌনমিলনে প্রলুব্ধ হতে পারত। অন্য পুরুষের প্রতি হারেমের নারীদের আকর্ষণ বোধ করা তো আর অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়।
(২) পরিবার বা সন্তান-সন্ততি-পরিবারহীন এসব খোজা পুরুষ মানুষরা অসহায় বৃদ্ধ বয়সে দেখাশোনার জন্য সামান্য সান্নিধ্যের আশায় মালিকের প্রতি চরম আনুগত্য প্রদর্শন করে নিজেদেরকে উৎসর্গ করে দিত। উপরন্তু যৌন তাড়নাবিহীন খোজাকৃত দাসরা সাধারণ যৌন উন্মাদনাযুক্ত ইসলামি সংস্কৃতিতে সহজেই একাগ্রভাবে কাজে মনসংযোগ করতে পারত।
(৩) খোজা ক্রীতদাসদের অত্যধিক চাহিদার আর-এক অন্যতম কারণ –শাসক, সেনাধ্যক্ষ ও সম্ভ্রান্তদের সমকামিতার প্রতি মোহাচ্ছন্নতা। ইন্দ্রিয়গত আকাক্ষা চরিতার্থ করার জন্য রাখা হত খোজাদের। সেইসব খোজাদের বলা হত ‘গেলেমান’ বা ‘গিলমান’। তাঁরা উৎকৃষ্ট ও আকর্ষণীয় পোশাকে সজ্জিত থাকত এবং নারীদের মতো তাঁদের শরীরকে সুন্দর করে রাখত। সুগন্ধী সহ প্রসাধনী করত।
.
হিজড়াসমাজে খোজাকরণ
হিজড়াসমাজে সাধারণত দু-রকমভাবে খোজা করা হয়। একটি হল— (১) Castration (Removal of the testicles), অপরটি (২) Penectomy (Penis Removal)। ক্যাসট্রেশন (Castration) হল আসলে পুরুষের ভাসডিফারেন্স বা শুক্রনালীকে কেটে দেওয়া হয়। এই শুক্রনালী শুক্রাণু বহন করে। কাজেই শুক্রাণু বীর্যে আসতে পারে না। কাজেই এই পুরুষের পক্ষে নারীর গর্ভসঞ্চার করানো হয় না। এটি পুরুষের স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, যা ভেসেকটমি বলে পরিচিত। ভেসেকটমি অপারেশনের পর সেই পুরুষের যৌন-ইচ্ছা, যৌনক্ষমতা, যৌন-আবেদন কোনোটাই হ্রাস পায় না। হারেমের খোজাদের বেশিরভাগেরই এই পদ্ধতিই অবলম্বন করা হত। তবে Penectomy খোজা হল পুরুষের লিঙ্গটাকে কেটে শরীর থেকে আলাদা করে ফেলা। বাৎসায়নের আগেই কৌটিল্য তাঁর ‘অর্থশাস্ত্র’-এ এক বিশেষ ধরনের পুরুষের কথা উল্লেখ করেছেন। এরা নপুংসক’। পুরুষাঙ্গ ছেদন করে এদের নপুংসক করা হত। এরা ছিল রাজ-অন্তঃপুরের পাহারাদার। শুধু মহিলারক্ষীদের এই করানো বেশ কঠিন ছিল। আবার পুরুষরক্ষীবাহিনীকে বিশ্বাস করা যেত না। এদের দ্বারা অতঃপুরবাসিনীর শ্লীলতাহানি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। কিছু পুরুষকে লিঙ্গ কেটে খোজা করে দেওয়া হয়। রাজ-অন্তঃপুরের বা হারেমের মহিলারা এইসব খোজাদের দিয়ে বিকৃতভাবে তাঁদের যৌনক্ষুধা মেটাতো। রাজা বা বাদশাও যাবে কেন? এঁদের অনেকেই পুরুষসঙ্গমে তৃপ্ত হতেন। লিঙ্গ কেটে ফেললে যৌনমিলন একেবারেই অসম্ভব।
হিজড়া-মহলে কীভাবে লিঙ্গ কর্তন খোজা (Penectomy) করা হয় সেটা এবার জানা যেতে পারে। বীভৎস নারকীয় এবং অবৈজ্ঞানিক উপায়ে লিঙ্গ শরীর থেকে কেটে ফেলা হয়। হিজড়া বানানোর জন্য নিয়ে আসা ব্যক্তিকে একটি নির্দিষ্ট ঘরে অন্তরীণ অবস্থায় ১১ দিন থাকতে হয়। সূর্যের আলো পর্যন্ত দর্শন করতে পারবে না সে। প্রথম প্রথম মহল্লার হিজড়ারা এর সঙ্গে খুব ভালো ব্যবহার করে। চলে আদর আর যত্ন। লিঙ্গচ্ছেদনের জন্য হবু হিজড়ার সম্পত্তি আদায় করে নেয়। যৌন পরিবর্তনকামীরা মত দিলেও অন্যরা মত দিতে রাজি হয় না। রাজি না-হলে চলে দৈহিক আর মানসিক নির্যাতন। এই সময়ে হবু হিজড়াকে প্রচুর পরিমাণে মাদক সেবন করানো হয়। অমানবিক অত্যাচার ও মাদকের প্রভাবে তার স্বাভাবিক চেতনা লুপ্ত হয়। ঠিক ১১ দিন পর অনেক রাতে মহল্লার দলপতি তার অনুগত কয়েকজনকে হিজড়াকে নিয়ে ওই ঘরে ঢোকে। নেশায় আচ্ছন্ন হবু হিজড়াকে উলঙ্গ করে হাত-পা বেঁধে দেয়ালের সঙ্গে চেপে ধরা হয়। যাতে চিৎকার করতে না-পারে সেজন্য মুখের ভিতর কাপড় জাতীয় কিছু খুঁজে দেওয়া হয়। এরপর কালো ফিতে দিয়ে লিঙ্গ ও অণ্ডকোশ একসঙ্গে সজোরে বেঁধে দু-দিক থেকে টেনে ধরা হয়। মাথা একদিকে হেলিয়ে কয়েকজন হিজড়া তাকে চেপে ধরে রাখে। এরপর দলপতি অত্যন্ত ধারালো ছুরি বা ক্ষুর দিয়ে ঘ্যাচাং করে লিঙ্গটি কেটে ফেলে। তখন প্রচুর পরিমাণে রক্ত নিঃসরণ হতে থাকে। হিজড়াদের ধারণা এই রক্তপাতের মধ্য দিয়ে শরীরের সমস্ত পুরুষ-রক্ত বেরিয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে শরীরে নারী-রক্তের জন্ম হয়। একে ওরা ‘নির্বাণ বলে। নির্বাণের মধ্য দিয়ে হিজড়ার জন্ম হয়।
সে যাই হোক, প্রসঙ্গে আসি। লিঙ্গচ্ছেদনের পর ওই ব্যক্তিকে চিৎ করে শুইয়ে তাঁর ক্ষতস্থানের নীচে একটি পাত্র রাখা হয়। ক্ষতস্থান থেকে বেরিয়ে আসা রক্ত ওই পাত্রে রাখা হয়। কর্তিত লিঙ্গটিও রাখা হয় ওই পাত্রটিতেই। পরদিন সকালে পাত্রটিকে ফুল দিয়ে সাজানো একটি ঝুড়ির মধ্যে নিয়ে হিজড়ারা মিছিল করে চলে কাছেপিঠের কোনো জলাশয়ে। সেখানেই ঝুড়িটি ভাসিয়ে দেওয়া হয়। ছেদনকার্যের পর নতুন হিজড়াকে ৪৮ ঘণ্টা ঘুমোতে দেওয়া হয় না। ক্ষতস্থান রক্ত বন্ধ করার জন্য ঘুঁটে পোড়া ছাই খয়ের ভিজিয়ে পুরু করে ওই ক্ষতস্থানের ছাইয়ের উপর লাগিয়ে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই জায়গাটি প্লাস্টারের মতো শক্ত হয়ে যায়। নির্মাণ হয় এক লিঙ্গ-কবন্ধ হিজড়া।
লিঙ্গ কর্তনের পর আর-একটি প্রধান কাজ হল স্তন-দুটিকে পুষ্ট করা। এটি হিজড়াসমাজের অত্যন্ত গোপনে হয়, যাকে বলে ট্রেড সিক্রেট। লিঙ্গ কর্তনের কয়েকদিন পর নতুন হিজড়া একটু সুস্থ হয়ে উঠলে মহল্লার দলপতি তাকে Lyndiol (চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া এই ট্যাবলেট খাওয়া অনুচিত) নামে এক ধরনের জন্ম নিরোধক ট্যাবলেট খাওয়ায়। বেশ কয়েক মাস ধরে এই ট্যাবলেট সেবন করানো হয় রোজ, নিয়মিত। এই ট্যাবলেটে ইথিলিন অস্ট্রাডাইওলের পরিমাণ একটু বেশি থাকে। ফলে শরীরে ইস্ট্রোজেন হরমোনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। হরমোনের কু-প্রভাবে স্তনগ্রন্থিতে স্নেহজাতীয় পদার্থ সঞ্চিত হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে পুরুষ-বক্ষ থেকে নারী-স্তনের মতো স্ফীত ও পরিপুষ্ট হতে থাকে। নারীদের মতোই স্তনবৃন্তও ফুলে ওঠে।তবে যাদের আর্থিক সামর্থ্য থাকে তারা প্ল্যাস্টিক সার্জারির মাধ্যমে স্তন প্রতিস্থাপন বা সিলিকন ব্রেস্ট করিয়ে নেয়। খুবই ব্যয়সাপেক্ষ এই পদ্ধতি আমাদের দেশের মতো তৃতীয় বিশ্বে প্রায় অসম্ভব হলেও ধনতান্ত্রিক দেশগুলির হিজড়ারা সিলিকন ব্রেস্ট বানিয়ে নেয়। তবে তারা কিন্তু সকলেই লিঙ্গ কর্তন করে না। নীল ছবির দুনিয়ায় এদের বেশ কদর আছে। এরা ‘shemale’ বা ‘Ladyboy’। তবে সোমনাথ ওরফে মানবী মনে করেন, “মেয়ে হিজড়ে ছেলে হিজড়ে বলে কিছুই নেই। সকলেই সমান হিজড়ে। হিজড়ে দলে দু-রকম মানুষ –আকুয়া আর নির্বাণ। আকুয়ারা পেনিস টেসটিস এখনো কেটে ফেলে দেয়নি, আর নির্বাণ হল তাঁরাই যাঁরা কেটে ফেলে দিয়েছে”।
.
হিজরাদের দেবতা
বহুচেরা মাতা হলেন হিজড়াদের দেবতা। হিন্দু হিজড়াদের এই দেবতার জনপ্রিয় মূর্তিটিতে দেখা যায়, তিনি একটি মোরগের পিঠে বসে আছেন এবং হাতে ধরে আছেন একটি তরবারি, ত্রিশূল ও একটি বই। বহুচারা সংক্রান্ত কাহিনিগুলিতে পুরুষাঙ্গ কর্তন ও শারীরিক যৌন বৈশিষ্ট্যের অন্যান্য পরিবর্তনের বেশ কিছু উদাহরণ পাওয়া যায়। এই জন্যে তাঁকে পুরুষের প্রতি অভিশাপদাত্রীর দেবী মনে করা হয়। কথিত আছে, বহুচারা ছিলেন এক নশ্বর নারী। তিনি শহিদ হন। একটি কাহিনিতে দেখা যায়, একদল দস্যু বহুচারাকে ধর্ষণ করার জন্য আক্রমণ করেছিল। সে সময় বহুচারা নিজের তরবারিতেই নিজেরই স্তন দুটি কর্তন করে ফেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হয়। অন্য একটি কাহিনিতে জানা যায়, বহুচারার স্বামী যখন একটি উপবনে সমকামী রতিক্রিয়ায় লিপ্ত ছিলেন, তখন বহুচারা তাঁকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। তখন স্বামীর পুরুষাঙ্গ খসে পড়ে এবং তিনি নারীর বেশ ধারণ করতে বাধ্য হন।
বহুচারার উপাখ্যানগুলিতে তাঁর দৈবসত্ত্বা পাওয়ার পর লিঙ্গ পার্থক্যের বিষয়টি লক্ষিত হয়। একটি কিংবদন্তী অনুসারে, এক রাজা বহুচারার কাছে পুত্রসন্তান কামনা করেছিলেন। বহুচারা তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। কিন্তু বড়ো হয়ে রাজকুমার সন্তান উৎপাদনে অক্ষম হন। এক রাতে বহুচারা রাজকুমারকে স্বপ্নে দেখা দেন এবং আদেশ করেন যাতে সে পুরুষাঙ্গ কর্তন করে নারীর বেশ ধারণ করেন এবং তাঁর দাসত্ব করেন। প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে, বহুচারা এরপরও পুরুষত্বহীন পুরুষদের চিহ্নিত করে লিঙ্গ কর্তন করতে আদেশ দিতে থাকেন। যাঁরা সেটা করতে অস্বীকার করে তিনি তাঁদের শাস্তি দেন। ফলে তাঁরা পরবর্তী সাত জন্ম পুরুষত্বহীন হয়ে থাকে। এই কাহিনিটিই বহুচারা কাল্টের উৎস। বহুচারা ভক্তদের নিজেদের পুরুষাঙ্গ কর্তন করে আজীবন “ব্রহ্মচারী’ থাকতে হয়।
বহুচারা মন্দিরে ‘কমলিয়া’ নামে এক বিশেষ হিজড়া সম্প্রদায় আছে। এরা পুরুষ। এরা একই সঙ্গে নিজেদের নারী ও পুরুষ হিসাবে কল্পনা করে। তাই লম্বালম্বিভাবে দেহের এক অংশে পুরুষের পোশাক এবং অপর অংশে নারীর বেশ ধারণ করে। এই ‘কমলিয়া’ ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে।
.
রূপান্তরকামী
রূপান্তরকামীর উদাহরণ হিসাবে হাতের সামনে জ্বলজ্বল করছে সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামটি। যিনি আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে পুরুষ শরীর ত্যাগ করে নারী শরীর গ্রহণ করেছেন। সন্তানধারণ করার ক্ষমতা ছাড়া তিনি আজ পূর্ণাঙ্গ নারীতে রূপান্তরিত। তাঁর বর্মান নাম মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়। ঈশ্বর তাঁকে এক পুরুষের শরীর দিয়ে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে মনকেই জিতিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ২০০৩ সালে একটি লিঙ্গ পুনর্নির্মাণ সার্জারি করিয়েছিলেন তিনি, তাঁর মনের সঙ্গে শরীরেও বসত করতে লাগল এক মানবী’। এরপর সমাজের বুকে নিজের অস্তিত্বই শুধু টিকিয়ে রাখা নয়, মানুষের মধ্যে রীতিমতো চর্চিত হতে শুরু করেন মানবী। এরপর ২০০৫ সালে বাংলা সাহিত্যে পিএইডি অর্জনকারী দেশের প্রথম রূপান্তরকামী হলেন এই মানবী। এরপর ২০১৫ সালে তিনি প্রথম রূপান্তরকামী অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত হন কৃষ্ণনগর ওম্যানস কলেজে। বর্তমানে তিনি ঢোসা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের দায়ভার সামলাচ্ছেন। একটি সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে মানবী বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন যে, তাঁর এই মেয়ে জীবনকে তাঁর বাবা কখনোই মেনে নিতে পারেননি। তাঁকে বরাবরই তিরস্কার সহ্য করতে হয়েছে, কিন্তু জীবনের লড়াইয়ে পিছিয়ে যাননি মানবী। দীর্ঘদিনের সংগ্রাম আজ তিনি অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছেন।
রূপান্তরকামিতা (Transsexualism) বলতে বিশেষ একটি প্রবণতা বোঝায়, যখন সেক্স বা ‘জৈব লিঙ্গ’ ব্যক্তির জেন্ডার বা ‘সাংস্কৃতিক লিঙ্গ’-এর সঙ্গে সংঘর্ষ তৈরি করে। রূপান্তরকামী মানুষরা এমন একটি যৌন-পরিচয়ের (Sex Identity) অভিজ্ঞতা লাভ করেন যা ঐতিহ্যগতভাবে তাঁদের নির্ধারিত যৌনতার সঙ্গে সমঝতা করতে সক্ষম নয় এবং স্থিতিশীলও নয়। অতএব নিজেদেরকে স্থায়ীভাবে সেই লিঙ্গে পরিবর্তন করতে চান। রূপান্তরকামী মানুষেরা পুরুষ হয়ে (বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যে) জন্মানো সত্ত্বেও মনমানসিকতায় নিজেকে নারী ভাবেন, পুরুষের প্রতি যৌনাকৃষ্ট হন। অপরদিকে নারী হয়ে জন্মানোর পরও মানসিক জগতে নিজেকে পুরুষ বলে মনে করেন, নারীর প্রতি যৌনাকৃষ্ট হন। এঁদের কেউ কেউ বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরিধান করেন, এই ব্যাপারটিকে বলা হয় (ট্রান্সভেস্টিজম বা ক্রসড্রেস)। আবার কেউ সেক্স রিঅ্যাসাইনমেন্ট সার্জারির মাধ্যমে রূপান্তরিত মানবে (Transexual) পরিণত হন। এরা সকলেই রূপান্তরিত লিঙ্গ নামক বৃহৎ রূপান্তরপ্রবণ সম্প্রদায়ের (Transgender) অংশ হিসেবে বিবেচিত।
শুধু মানুষ নয়, বিজ্ঞানীরা প্রাণিজগতের মধ্যেও রূপান্তরকামিতার উপস্থিতি লক্ষ করেছেন। প্রাণীবিজ্ঞানীরা উত্তর আমেরিকার সমুদ্রোপকূলে আটলান্টিক স্লিপার শেল (Atlantic slipper shell) নামে পরিচিত ক্রিপিডুলা ফরমিক্যাটা (Crepidula_Fornicata) এবং ল্যাবারিডেস ডিমিডিয়াটাস (Laborides dimidiatus), ইউরোপিয়ান ফ্লে অয়েস্টার (European Flay Oyster) ও অস্ট্রা এডুলিস (Ostrea edulis) প্রজাতির ঝিনুকের মধ্যে রূপান্তরকামিতা এবং লিঙ্গ পরিবর্তনের প্রমাণ পেয়েছেন। যৌনতার পরিবর্তন ঘটে মাছি, কেঁচো, মাকড়শা এবং জলজ ফ্রি ডাফনিয়াদের বিভিন্ন প্রজাতিরে মধ্যেও। লিঙ্গ পরিবর্তনকারী মাছের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে প্রবালের খাঁজে বসবাসকারী গ্রুপার মাছ। এ গ্রুপার মাছ প্রথমে স্ত্রী হিসাবে জন্মগ্রহণ করে ও পরিপক্কতা লাভ করে এবং এক বা একাধিকবার প্রজননে অংশ নেয়। এসব স্ত্রী মাছ পরে লিঙ্গ পরিবর্তন করে পুরুষ মাছে রূপান্তরিত হয় এবং সক্রিয় পুরুষ মাছ হিসাবে প্রজননে অংশগ্রহণ করে। ক্লাউনফিশও রূপান্তরকামিতার অন্যতম উদাহরণ—
জন্মগতভাবে সকল ক্লাউনফিশ পুরুষ, কিন্তু দলের সবচেয়ে বড়ো আকারের মাছটি নারী মাছে রূপান্তরিত হয়। ভেটকি বা কোরাল মাছও ওইভাবে লিঙ্গ পরিবর্তন করে বলে জানা যায়।
মানবসভ্যতার বিভিন্ন সমাজব্যবস্থায় লিখিত ইতিহাসের সমগ্র সময়কাল জুড়ে রূপান্তরকামিতার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে আমেরিকার পুরুষ রূপান্তরকামী জর্জ জরগেন্সেনের ক্রিস্টিন জরগেন্সেনের রূপান্তরিত হওয়ার কাহিনি মিডিয়ায় এক সময় আলোড়ন তুলেছিল। এছাড়া জোয়ান অব আর্ক, জীববিজ্ঞানী জোয়ান (জনাথন) রাফগার্ডেন, বাস্কেটবল খেলোয়াড় ডেনিস রডম্যান, চক্ষুচিকিৎসক এবং পেশাদার টেনিস খেলোয়াড় ডঃ রেনি রিচার্ডস, সঙ্গীতজ্ঞ বিলিটিপটন সহ অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির মধ্যে রূপান্তরপ্রবণতার উল্লেখ ইতিহাসে মেলে। ১৯৬০ সালে মনোচিকিৎসক ওয়ালিন্দার রূপান্তরকামীদের উপরে একটি সমীক্ষা চালান। তার এই সমীক্ষা থেকে জানা যায় প্রতি ৩৭ হাজারে একজন পুরুষ রূপান্তরকামীর জন্ম হচ্ছে। অপরদিকে প্রতি ১০৩,০০০-এ একজন স্ত্রী রূপান্তরকামীর জন্ম হচ্ছে। ইংল্যান্ডে এই সমীক্ষাটি চালিয়ে দেখা গেছে যে সেখানে প্রতি ৩৪ হাজারে একজন পুরুষ রূপান্তরকামী ভূমিষ্ট হচ্ছে, অপরদিকে প্রতি ১০৮,০০০-এ একজন জন্ম নিচ্ছে একজন স্ত্রী রূপান্তরকামী। অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডে গবেষণা করে দেখা গেছে সেখানে ২৪ হাজারে পুরুষের মধ্যে একজন এবং ১৫০,০০০ নারীর মধ্যে একজন রূপান্তরকামীর জন্ম হয়।
সমাজবিজ্ঞানী অ্যান ওকলের মতে, জৈবিক লিঙ্গ শারীরিক বৈশিষ্ট্য বহন করে। আর মানসিক লিঙ্গ’ একটি নির্দিষ্ট সমাজে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে নির্ধারিত বিশিষ্টতা নির্দেশ করে। একজন নারী ও পুরুষের কার কী রকম পোশাক-পরিচ্ছদ হবে; কে কী রকম আচার-আচরণ করবে; আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা কার কী রকম হবে; সমাজের নানা ধরনের কাজে একজন নারী বা একজন পুরুষের ভূমিকা কী হবে এই বিষয়গুলো নির্ধারণ করে জেন্ডার বা লিঙ্গ। অর্থাৎ, ‘জৈবিক লিঙ্গ’ বিষয়টি পুরোপুরি শরীরের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু মানসিক লিঙ্গ নির্ভরশীল সমাজের উপর। যেহেতু নারী বা পুরুষের দায়িত্ব, কাজ ও আচরণ মোটামুটি সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত হয়। তাই সমাজ পরিবর্তন বা সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জেন্ডারের ধারণা বদলে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আমরা যখন কাউকে ‘নারী’ বা ‘পুরুষ’ হিসাবে চিহ্নিত করি, তখন সেখানে ‘জৈবিক লিঙ্গ’ নির্দেশ করাটাই মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু ‘মেয়েলি’ বা ‘পুরুষালি ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে জেন্ডার প্রপঞ্চকে যুক্ত করা হয়, যেখানে নারী বা পুরুষের লৈঙ্গিক বৈশিষ্ট্যকে ছাপিয়ে স্বভাব আচরণগত ইত্যাদি বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। আর এই কারণে সেক্সকে জৈবলিঙ্গ এবং জেন্ডারকে সামাজিক বা ‘সাংস্কৃতিক লিঙ্গ’ বলে অনেকে অভিহিত করেন। বস্তুত জৈব বৈশিষ্ট্যের বলয় অতিক্রম করে সাংস্কৃতিক বলয়ে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার বাসনার কারণেই মানব সমাজে রূপান্তরকামিতার অস্তিত্ব আছে বলে মনে করা হয়।
অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে লিঙ্গ পরিবর্তন বা সেক্সচেঞ্জ একটি খুব জটিল প্লাস্টিক সার্জারি অপারেশন। এই অপারেশনে যাঁরা নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে আছেন হ্যারি বেঞ্জামিন, স্টিক, আব্রাহাম, জন মানি প্রমুখ। রূপান্তরকামী এবং উভলিঙ্গ মানুষদের চাহিদাকে মূল্য দিয়ে ডাক্তাররা সার্জারির মাধ্যমে সেক্সচেঞ্জ অপারেশন করে থাকেন। যে সকল রূপান্তরকামী একে অসুখ মনে করেন না, তাঁদের ঔষধ প্রয়োগ করে উক্ত মানসিকতাকে বদলে ফেলা সম্ভব হয় না। এঁদের অনেকেই সেক্সচেঞ্জ অপারেশনের মধ্য দিয়ে মানসিক পরিতৃপ্তি পেয়ে থাকেন। পুরুষ রূপান্তরকামী অর্থাৎ যাঁরা পুরুষ থেকে নারীতে রূপান্তরিত হতে চায়, তাঁদের জন্য এক ধরনের অপারেশন। আর নারী রূপান্তরকামীদের জন্য ভিন্ন অপারেশন রয়েছে। মুলত শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে চামড়া ও টিস্যু নিয়ে গ্রাফটিংয়ের মাধ্যমে যৌনাঙ্গ গঠন করা হয়, হরমোন থেরাপির সাহায্যে স্তন গ্রন্থির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো হয়, সিলিকন টেস্টিকেলের সাহায্যে অণ্ডকোশ তৈরি করা হয়।
ইরানে ১৯৭৯ সালে ইসলামিক বিপ্লবের আগে লিঙ্গ-পরিবর্তনের প্রবণতা সরকার স্বীকার করেনি। অবশেষে ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে সরকার লিঙ্গ-পরিবর্তনকারীদের স্বীকার করে নেয় ও তাঁদের শল্যচিকিৎসার অনুমোদন দেয়। ২০০৮ সালের মধ্যে ইরান বিশ্বের অন্য দেশগুলোর চেয়ে অনেক বেশি এ জাতীয় শল্যচিকিৎসা করে। একমাত্র থাইল্যান্ডই শুধু তাঁদের চেয়ে এগিয়ে থাকে। যাঁদের সাহায্য প্রয়োজন তাঁদেরকে সরকার অর্ধেক টাকা দেয় শল্যচিকিসাত্র জন্য ও তা জন্ম সনদেই লেখা থাকে। ১৯৬৩ সালে ইরানের আয়াতুল্লাহ রহোল্লাহ খোমেইনি তাঁর লেখা এক গ্রন্থে বলেন যে, লিঙ্গ পরিবর্তন ইসলামবিরোধী নয়। সে সময় আয়াতুল্লাহ ছিলেন যুগান্তকারী, শাহবিরোধী বিপ্লবী এবং তাঁর এই ফতোয়া সে সময়ের রাজকীয় সরকার কোনো আমলে নেয়নি ও তাঁদের এই বিষয়ে কোনো নীতি ছিল না। ১৯৭৯ সালের বিপ্লবের পর ইরানে নতুন ধর্মীয় সরকার আসে যাঁরা লিঙ্গ-পরিবর্তনকে পুরুষ সমকামী ও স্ত্রী সমকামীদের একই সারিয়ে দাঁড় করিয়ে এটা নিষিদ্ধ করে ও এর জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান ঘোষণা করে। লিঙ্গ পরিবর্তনের স্বপক্ষে প্রথম প্রচারণা চালান ফেরেয়দুন নামের একজন পুরুষ, যিনি মেয়ে হয়ে যান লিঙ্গ-পরিবর্তন করে। নতুন নারী-জীবনে তিনি মারইয়াম হাতুন মোল্কারা নাম ধারণ করে। বিপ্লবের আগে তিনি মেয়ে হয়ে যান, কিন্তু তিনি শল্যচিকিৎসার কোনো চেষ্টা করেননি। পরে তিনি ধর্মীয় অনুমোদন চান। ১৯৭৫ সালে থেকে তিনি আয়াতুল্লাহ কাছে বার বার চিঠি লিখতে থাকেন যিনি ওই বিপ্লবের নেতা ছিলেন ও নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিপ্লবের পর তিনি চাকরিচ্যুত হন ও তাঁকে জোর করে হরমোন ইঞ্জেকশন দেওয়া হতে থাকে। তিনি কারারুদ্ধও হন। পরে তিনি মুক্তি পান তার পরিচিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে ও লবিং চালাতে থাকেন নেতাদের কাছে। তিনি খোমেইনির সঙ্গে দেখা করতে যান। তখন তাঁর রক্ষীরা তাঁকে থামান ও মারতে থাকেন। পরে আয়াতুল্লাহ তাঁকে এক চিঠির মাধ্যমে বিষয়টির বৈধতা দান করেন। এ ধরনের শল্যচিকিৎসার পক্ষে ফতোয়া হিসাবে চিঠিটিকে চিহ্নিত করা হয়।
উভলিঙ্গ মানবদের ইংরেজিতে অভিহিত করা হয় হার্মফ্রোডাইট বা ইন্টারসেক্স (আন্তঃলিঙ্গ) হিসাবে। উভলিঙ্গত্বকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়– (১) প্রকৃত উভলিঙ্গত্ব (true-hermaphrodite) এবং (২) অপ্রকৃত উভলিঙ্গত্ব (pseudo-hermaphrodite)। প্রকৃত উভলিঙ্গ হচ্ছে যখন একই শরীরে স্ত্রী এবং পুরুষ যৌনাঙ্গের সহাবস্থান থাকে। তবে প্রকৃতিতে প্রকৃত উভলিঙ্গত্বের সংখ্যা খুবই কম। বেশি দেখা যায় অপ্রকৃত উভলিঙ্গত্ব। যখন কোনো ব্যক্তি এক যৌনতার প্রাইমারি বা প্রাথমিক যৌন বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্ম নেয়, কিন্তু অপর যৌনতার সেকেন্ডারি বা গৌণ যৌন বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেড়ে উঠতে থাকে, তখন তাকে অপ্রকৃত উভলিঙ্গত্ব বলে। সাধারণত ছয় ধরনের অপ্রকৃত উভলিঙ্গত্ব দৃশ্যমান –(১) কনজেনিটাল এড্রেনাল হাইপারপ্লাসিয়া (CAH), (২) এন্ড্রোজেন ইন্সেন্সিটিভিটি সিনড্রোম (AIS), (৩) গোনাডাল ডিসজেনেসিস, (৪) হাইপোস্পাডিয়াস, (৫) টার্নার সিনড্রোম (xo) এবং (৬) ক্লাইনেফেল্টার সিনড্রোম (XXY)। উভলিঙ্গত্বের বিভিন্ন প্রপঞ্চের উদ্ভব বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে।
রূপান্তরকামী পুরুষ এমন এক ব্যক্তিত্ব যাকে জন্মের সময় স্ত্রী হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছিল। বিভিন্ন ধরনের লিঙ্গ বৈকল্পিক মানুষ (রূপান্তরকামীরা সহ) ট্রান্সজেন্ডার শব্দের অন্তর্ভুক্ত। অনেক রূপান্তরকামী পুরুষ অস্ত্রোপচার বা হরমোন রূপান্তর বা উভয়ভাবেই তাঁদের শরীর এমনভাবে পরিবর্তিত করেন যাতে তাঁদের গঠন তাদের লিঙ্গ পরিচয়ের সঙ্গে অভিন্ন হয় বা লিঙ্গ অস্বস্তিকে হ্রাস করে।
গবেষণা দেখায় গেছে যে বেশিরভাগ রূপান্তরকামী পুরুষরা বিপরীতকামী হয়ে থাকেন (যার অর্থ তাঁরা নারীদের প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করেন) মূলত রূপান্তরকামী পুরুষ শব্দটি এমন মহিলা থেকে পুরুষ রূপান্তরকামী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে ব্যবহার করা হত, যাঁরা হরমোন প্রতিস্থাপন চিকিৎসা বা লিঙ্গ পুনর্নির্মাণ অস্ত্রোপাচার বা উভয়ই করিয়ে থাকতেন। রূপান্তরের সংজ্ঞাটিকে মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের তত্ত্বগুলি বা স্বগ্রহণযোগ্যতার পদ্ধতিগুলিকে অন্তর্গত করার মাধ্যমে প্রসারিত করা হয়েছে। যাঁরা রূপান্তরকামী হিসাবে চিহ্নিত হন তাদের অনেকে লিঙ্গ অস্বস্তির শিকার হতে পারেন।
কয়েকটি পদক্ষেপগুলিই রূপান্তরের অংশ হতে পারে। যেমন –(১) সামাজিক রূপান্তর: নিজস্ব পছন্দসই নাম এবং সর্বনাম ব্যবহার করা, লিঙ্গ উপযুক্ত পোশাক পরিধান করা, পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং সাধারণত কর্মক্ষেত্রে/বিদ্যালয়ে স্বরূপ প্রকাশ। (২) লিঙ্গ পুনর্নির্মাণ চিকিৎসা: হরমোন প্রতিস্থাপন চিকিৎসা (এইচআরটি), অথবা অস্ত্রোপাচার (এসআরএস)। (৩) আইনি বিবৃতি: দলিলগুলিতে নাম এবং (কখনও কখনও) লিঙ্গ চিহ্ন পরিবর্তন করা। অবশ্য কিছু রূপান্তরকামী পুরুষ বিপরীতকামী মহিলাদের সঙ্গে সম্পর্কে থাকেন, আবার কিছু রূপান্তরকামী পুরুষরা কুইয়ার মহিলাদের সঙ্গে সম্পর্কে থাকেন। কারণ কুইয়ার মহিলারা বেশিরভাগ সময় অন্তরঙ্গ সঙ্গী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির লিঙ্গ এবং যৌন শারীরবৃত্ত বিষয়ে কম চিন্তিত হন। লেসবিয়ান সম্প্রদায়ের সঙ্গে রূপান্তরকামী পুরুষদের ইতিহাস থাকতে বা বিস্তৃত লিঙ্গ বৈচিত্র্যের গ্রহণযোগ্যতার কারণে তাঁরা এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে আরও ভালোভাবে মেলামেশা করতে পারেন। কিছু রূপান্তরকামী পুরুষ লেসবিয়ান হিসাবে চিহ্নিত হন, যাদের “বুচ লেসবিয়ান’ বলা হয়। এটা বুঝতে পারার আগে যে তাঁরা আসলে রূপান্তরকামী।
হুবার্ড একজন রূপান্তরকামী মানুষ। হুবার্ড মেয়েদের ৮৭ কেজি সুপার হেভিওয়েট বিভাগে নেমেছিলেন। তাঁর বয়স তখন ৪৩ বছর। তিনিই ছিলেন টোকিও অলিম্পিকের সব চেয়ে বেশি বয়সি প্রতিদ্বন্দ্বী। অলিম্পিকে যাওয়ার জন্য ছাড়পত্র পেয়েছিলেন হুবার্ড। তারপর তিনি জানিয়েছিলেন, নিউজিল্যান্ডের এত মানুষ তাঁকে সমর্থন করেছেন দেখে তিনি কৃতজ্ঞ ও আপ্লুত। এই রূপান্তরকামী অ্যাথলিট বলেছেন, তিন বছর আগে কমনওয়েলথ গেমসে যখন তাঁর হাত ভেঙেছিল, তখন অনেকেই বলেছিলেন, তাঁর কেরিয়ার শেষ হয়ে গেল। কিন্তু মানুষের সমর্থনে তিনি আবার ফিরে আসতে পেরেছেন। রূপান্তরকামী অ্যাথলিটদের জন্য আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির কিছু শর্ত আছে। হুবার্ড সেই সব শর্ত পূরণ করছেন। তিনি ২০১৩ সালে ৩৫ বছর বয়সে লিঙ্গ পরিবর্তন করেন।
নিউজিল্যান্ড অলিম্পিক কমিটির সিইও কেরেয়ন স্মিথ বলেছেন, হুবার্ড অলিম্পিক ও ইন্টারন্যাশনাল ওয়েটলিফটিং ফেডারেশনের সব শর্ত পূরণ করেছেন। তিনি বলেছেন, “আমরা স্বীকার করি যে, জেন্ডার আইডেনটিটি হল খুব জটিল ও স্পর্শকাতর বিষয়। এর সঙ্গে মানবাধিকার, সকলের জন্য সমান সুযোগের বিষয়টিও জড়িত। আর নিউজিল্যান্ড টিমে সকলকে নিয়ে চলার, সকলকে শ্রদ্ধা করার ঐতিহ্য আছে।” তবে কিছু নারী অ্যাথলিটের মতে, এর ফলে তাঁদের মেডেল জেতার সুযোগ কমে গেল। বেলজিয়ান ওয়েটলিফটার অ্যানা বলেছেন, হুবার্ডকে টোকিওতে সুযোগ দেওয়া নারী অ্যাথলিটদের কাছে একটা বড়ো প্রহসনের মতো। তাঁর মতে, “রূপান্তরকামীদের জন্য গাইডলাইন তৈরি করাটা কঠিন। কিন্তু যাঁরা এই সর্বোচ্চ পর্যায়ের জন্য নিজেকে তৈরি করেছে, তাঁরা জানেন, হুবার্ডের অন্তর্ভুক্তি কতটা অন্যায়।” হুবার্ড বলেছিলেন, “আমি জানি, সকলে আমাকে সমর্থন করবেন না। কিন্তু আমি আশা করি, মানুষ খোলা মনে বিচার করবেন। আমার এই জায়গায় আসতে অনেক সময় লেগেছে।”
.
সফল রূপান্তরকামী হিজড়া
আমরা এবার দেখব কয়েকজন সফল রূপান্তরকারী হিজড়া, যাঁরা জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। প্রথমেই আসব পদ্মীনি প্রকাশের কথায়। আর পাঁচজন রূপান্তরকামীর মতো পদ্মীনিও তাঁর পরিবারের কাছে চরম অবহেলার শিকার হয়েছিলেন। নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করে উঠতে না পেরে ১৩ বছর বয়সে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছিলেন তিনি। ছোটো থেকে সমস্যা যাঁর নিত্যসঙ্গী সেই পদ্মীনি একদিন ঘুরে দাঁড়ালেন। ২০১৪ সালে তিনি কোয়েম্বাটোরের একটি স্থানীয় টেলিভিশন চ্যানেলের প্রথম রূপান্তরকামী প্রাইম টাইম অ্যাঙ্কর হয়েছিলেন।
লক্ষ্মী নারায়ণ ত্রিপাঠি ২০০৮ সালে লক্ষ্মী নারায়ণ ত্রিপাঠি হলেন রাষ্ট্রসঙ্ঘের এশিয়া প্যাসিফিকের প্রথম রূপান্তকারী ভারতীয় প্রতিনিধি। কিন্তু তাঁর এই রূপান্তরকামিতার জন্য ছেলেবেলা থেকেই তাঁকে অসম্ভব লড়াই করতে হয়েছে। বর্তমানে তিনি একজন সমাজকর্মীও বটে। রূপান্তরিত সম্প্রদায়ের উন্নয়নকল্পে তিনি ২০০৭ সালে ‘অস্তিত্ব’ নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করেন। তাঁর কথায়, ‘একজন রূপান্তরিত মহিলা হিসাবে তাঁরা যেন পুরুষের হাতের খেলনা। আমাদের শ্লীলতাহানি করা যায়, আমাদের অপমান করা যায়। এমনকী আদালতও বলেছে যে, আমাদের নাকি শ্লীলতাহানি করা যায় না। এই পরিপ্রেক্ষিতে সেই পুরনো গল্প। লোকেরা আমাদের ছক্কা, হিজড়া বিভিন্ন নামেই ডাকতে পারে। আমাদের সম্প্রদায়ে হাজার হাজার নির্ভয়া আছে। আপনাদের কোনো ধারণা নেই আমাদের মধ্যে কতজনকে ধর্ষণ করে খুন করে দেওয়া হয়।”
কে প্রীতিকা ইয়াশিনি তামিলনাড়ুর প্রথম রূপান্তরকীমা পুলিশ অফিসার। পুলিশবাহিনীতে যোগ দেওয়া নিয়েও রীতিমতো যুদ্ধ করেছিলেন প্রীতিকা। আবেদনপত্রে ‘রূপান্তরকামী’ হিসাবে যোগ দেওয়ার জন্য রীতিমতো আইনি লড়াই লড়েছিলেন তিনি। তবে শেষপর্যন্ত অবশ্য তিনিই জয়ী হলেন। বর্তমানে তিনি চেন্নাইয়ে সাব-ইন্সপেকটার হিসাবে কর্মরত।
৬ প্যাক ব্যান্ড ভারতের প্রথম রূপান্তরকামী মিউজিক ব্যান্ড। ৬ সদস্যের রূপান্তরকামী মহিলার ২০১৬ সালে এই ব্যান্ডটি ‘কানস গ্র্যান্ড প্রিক্স গ্লাস লায়ন’ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন।
জয়িতা মণ্ডল হলেন ভারতের প্রথম রূপান্তরকামী বিচারক, যিনি ২০১৭ সালের অক্টোবরে উত্তরবঙ্গের লোক আদালতে নিযুক্ত হয়েছিলেন।
নিতাশা বিশ্বাস হলেন ভারতের প্রথম রূপান্তরকামী বিউটি কুইন। ২০১৭ সালে | তিনি এই খেতাব অর্জন করেছিলেন।
ভারতের প্রথম রূপান্তরকামী আইনজীবি হলেন সত্যাশ্রী শর্মিলা। ২০১৮ সালের জুন মাসে তিনি আইনজীবি হিসাবে কাজ শুরু করেন।
ভারতের প্রথম রূপান্তরকামী অপারেশন থিয়েটার টেকনিশিয়ান হলেন জিয়া। ২০১৮ সালের জুন মাস থেকে তিনি এই কাজে নিযুক্ত।
ভারতের প্রথম রূপান্তরকামী মহিলা যাজক এস্থার ভারতী। তিনি বর্তমানে বিয়েও দেন।
হিজড়াসমাজের রীতিনীতি
সামাজিক মূলস্রোত থেকে এই সমাজ সম্পূর্ণই বিচ্ছিন্ন। হিজড়াসমাজের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, ধর্মীয় অনুশাসন সবই আলাদা। প্রত্যেক হিজড়া মহল্লায় একজন দলপতি থাকেন। এরা ‘গুরু-মা’ ‘নান-গুরু মা’ বলে পরিচিত। এই গুরু-মাই দলের অভিভাবক। গুরু-মায়ের তত্ত্বাবধানে হিজড়ারা হল তাঁর শিষ্য, চেলা বা মেয়ে। অবাধ্য হওয়া তো দূরের কথা, শিষ্যেরা গুরু-মাকে খুবই মান্য করে। শিষ্যত্ব সংগ্রহ করা এবং তাঁকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে কাজে পাঠানো গুরু-মায়ের অন্যতম প্রধান কাজ। গুরু-মায়ের তত্ত্বাবধানে শিষ্যরা নাচ-গান বাজনা শিখতে থাকে। শুধু নাচ-গান-বাজনা শিখলেই হয় না, তালি দেওয়া শেখাটাও অত্যন্ত জরুরি। সবাই জানেন, হিজড়াদের তালি বিশেষ ধরনের। দুটি হাতের তালুকে ৯০ ডিগ্রি কোণ করে এই তালি দেওয়া হয়।
হিজড়া দুনিয়ার প্রচলিত রীতি অনুসারে প্রত্যেক গুরু-মায়ের কাজের কিছু নির্দিষ্ট এলাকা থাকে। এই এলাকায় তিনিই হলেন হিজড়াদের ‘বস’। হিজড়া মহল্লায় একজন গুরু-মায়ের অধীনে কতজন শিষ্য থাকবে তার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। তবে যেসব শিষ্যরা মহল্লায় স্থায়ীভাবে বসবাস করে তাঁরা হল ‘সাধারণ শিষ্য’। একই গুরু-মায়ের সাধারণ শিষ্যেরা একে অন্যের গুরু-বোন। গুরু-মায়ের অবর্তমানে তাঁর সম্পত্তির সমান অংশ পায় শিষ্যেরা। তবে অনেক সময় মৃত্যুর আগেই গুরু-মা তাঁর সমস্ত সম্পত্তি কোনো একজন শিষ্যকে উইল করেও দিয়ে যান।
হিজড়াদের জীবনজীবিকা
সাধারণত দেখা যায় গুরু-মার তত্ত্বাবধানে থেকেই সমস্ত হিজড়াদের কাজ করতে হয়। কমন সোসাইটিতে যখন একটা মানুষ হিজড়া হয়ে ওঠার কারণে ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ে, ব্যঙ্গবিদ্রূপ ও মানসিক ও শারীরিক নিপীড়নের মধ্যে পড়ে যায়, তখন এই গুরু-মাই যেন সাক্ষাৎ দেবদূত। এই দেবদূতরাই তাঁদের আশ্রয় দেয়, জীবনজীবিকা দেয়, মুক্তি দেয়, রক্ষা করে। গুরু-মার মতো সহনশীল ও দায়িত্ববান মানুষরা যদি না থাকতেন তাহলে সমস্ত তৃতীয় লিঙ্গদের হয়তো আত্মহননের পথ বেছে নিতে হত। যাই হোক, এই হিজড়া সোসাইটিতে নাম লেখানোর পর গুরু-মা তাঁদের জীবনজীবিকার সন্ধান দেন। জীবিকার একটা অংশ গুরু-মাকে দিতে হয়, বাকি অংশ হিজড়ার। হিজড়ার সেই অংশ থেকে একটা অংশ সন্তান হিসাবে বাবা-মাকে পাঠান।
স্বাভাবিক মানুষদের মতো হিজাড়ারাও নানাবিধ পেশায় যুক্ত থাকে, যদিও সীমিত ক্ষেত্র। দেখা যাক— (১) বাচ্চা নাচানোই এদের প্রধান জীবিকা। সাধারণত বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে নবজাতকের জন্মের কথা ওরা জানতে পারে। তারপর একদিন দলবল নিয়ে হাজির হয় নবজাতকের বাড়িতে। বাচ্চাকে কোলে নিয়ে শুরু হয় নাচা-গানা। বাচ্চা নাচানোর পর ওরা যে টাকাপয়সা ও অন্যান্য দ্রব্য দাবি করে, তা বেশিরভাগ সময়ই জুলুমের পর্যায়ে পৌঁছে যায়। প্রাপ্য দাবি না-মিটলে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি এবং অশ্রাব্য গালিগালাজ দিয়ে নবজাতকের পরিবারকে হেনস্থা করতে থাকে। এই ঔদ্ধত্য ও দুর্বিনীত আচরণ শেষপর্যন্ত বাক্-বিতণ্ডা এবং হাতাহাতি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। বাচ্চা নাচিয়ে যে অর্থ উপার্জন হয় তার অর্ধেক গুরু-মা ও অর্ধেক শিষ্যারা পায়। অবশ্য কোনো কোনো অঞ্চলে উপার্জিত অর্থের এক-চতুর্থাংশ শিষ্যেরা পায়। তবে সব হিজড়াই যে জুলুমবাজি করে একথা বলা যায় না। আমার বাচ্চাকে যে হিজড়াদের দল নাচাতে এসেছিল তাঁরা জুলুমবাজি তো দূরের কথা, কোনো দাবি করেনি। সামর্থ্য অনুযায়ী যা দিয়েছিলাম সেটাই নিয়েছিল। (২) গুরু মায়েরা দালাল মারফৎ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে সুশ্রী ‘নাগিন’ হিজড়াদের পাঠিয়ে থাকে। দালালরা এদের নিয়ে তোলে ওইসব অঞ্চলের কিছু ব্যক্তির কাছে, যারা মাস্টারজি’ নামে পরিচিত। এই মাস্টারজিদের তত্ত্বাবধানে নাগিনরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে হিন্দি ফিল্মি দুনিয়ার চিত্তবিনোদক নৃত্য পরিবেশন করে। এইভাবে যে অর্থ উপার্জন হয় তার সিংহভাগই মাস্টারজির পকেটে চলে যায়। গুরু-মায়েরও দালালদের মাধ্যমে এই অর্থের একটা বড় অংশ লাভ করেন। (৩) মূল্য না দিয়ে বাজার থেকে সবজি-তরিতরকারি জোর করে তুলে নেয়। এই ‘তোলা’ তোলা ব্যবস্থা বহু বছর ধরে চলে আসছে। আজকাল দূরপাল্লার ট্রেনে ও বাসেও এঁদের তোলা তুলতে দেখা যায়। সবাই জোর করে তোলা তোলে না। অনেকেই আছেন মানুষ খুশি হয়ে যা দেয় তাতেই আশীর্বাদ করে। (৪) আন্তর্জাতিক চোরাচালানের সঙ্গেও হিজড়ারা যুক্ত থাকে। বিভিন্ন স্মাগলার ডনদের আন্ডারে কিছু গ্যাংলিডার আছে। সেই গ্যাংলিডারদের একটা বড়ো অংশই হিজড়া। (৫) হিজড়াদের একটা অংশ দেহ ব্যাবসার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে অর্থ ও যৌনসুখের আশায়। সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাষায়, “হিজড়াদের একমাত্র জ্বালা-যন্ত্রণা-প্রতিহিংসার বিষয় হল– নরনারীর ‘স্বাভাবিক জীবন’।” গণিকাপল্লি সত্যিকারের মেয়েদের হারিয়ে ‘পারিক’ হিজড়াদের চাহিদা বেড়েছে। কম বয়সি হিজড়ারা কলগার্ল হিসাবেও যৌনপেশায় লিপ্ত থাকে। হিজড়া মহল্লার বাইরে সমকামী অ্যাকটিভ পুরুষের কাছে হিজড়াদের বেশ চাহিদা আছে। এঁরা নারীর স্থলাভিষিক্ত পুরুষ যৌনকর্মী। মুম্বাই শহরে হিজড়াদের উপর বিশেষ অনুসন্ধান চালিয়ে ডাঃ ঈশ্বর গিলাডা এক সমীক্ষায় বলেছেন –সেখানকার প্রায় ৬০ শতাংশ হিজড়া বেঁচে থাকার তাগিদে বেশ্যাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তবে হিজড়ারা চায় তাঁরা আর পাঁচজনের কাজ করে জীবন চালায়। মানুষ তাঁদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ দিক। তাঁদের বক্তব্য– “এখন যে কাজ করি তাতে হয়তো কোর্মা-পোলাও-বিরিয়ানি খেতে পারি। তখন রোজগার অল্প হলেও ডাল-ভাত আলু সেদ্ধ খাব। তবু বুঝব ন্যায্য কামাইয়ে খাই।” বাংলাদেশ সরকার হিজড়াদের ভাতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিল বটে। কিন্তু সেই ভাতার টাকা হিজড়া হাতের তালু পর্যন্ত পৌঁছোয়নি।
হিজড়াদের যৌনকর্ম
আমাদের সমাজে লিঙ্গভিত্তিক দুই প্রকারের হিজড়া দেখতে পাই। যেমন– নারী হিজড়া ও পুরুষ হিজড়া। নারী হিজড়ারা পুরুষের সঙ্গেই যৌনকর্ম করতে চায়। একজন সত্যিকারের ভালোবাসার মানুষের অপেক্ষা করে থাকে। সেই স্বপ্নের পুরুষটির সঙ্গে সারাজীবন ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু সেই স্বপ্ন সবার পূরণ হয় না। কিন্তু বেশিরভাগ পুরুষরাই তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করে। ভালোবাসার অভিনয় করে তাঁদের শরীর ভোগ করে পালিয়ে যায়। বাংলাদেশের আপন নামের জনৈকা মেয়ে হিজড়া দাবি করেন “একজন মেয়ে পুরুষকে যতটা সুখ দিতে আমরা তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি সুখ দিতে পারি”। তিনি বলেন– “আমার শরীরের সব পার্টস ন্যাচারাল। আমার উপরতলা ও নীচতলা কোনোটাই কৃত্রিম নয়। আমার স্তন সিলিকনের নয়, অরিজিনাল। কারণ আমি একজন মেয়ে হিজড়া।” আপন বেশ্যাবৃত্তি করে অর্থ রোজগার করে না। দোকান কালেকশনই তাঁর মূল জীবিকা। ভালোবেসে এক রিকশাচালককে বিয়ে করেছিলেন। সেই রিকশাচালক বেশ কিছুদিন তাঁর সঙ্গে ঘরসংসার করে পালিয়ে যায়। আপন বলেন –“মানুষের যৌন চাহিদা থাকাটা স্বাভাবিক চাহিদা। আমারও আছে। কিন্তু সেই চাহিদা মেটাতে বহুগামিতায় যাব না। মনের মানুষ পেলে তাঁকে আমার সব উজাড় করে দেব।” আপনকে নিয়ে বাংলাদেশের ইউটিউবারদের কৌতূহলের সীমা অন্তহীন। ছবিতে যেমন দেখছেন ঠিক সেইভাবেই ইউটিউবারদের সামনে ক্লিভেজ প্রদর্শন করে বার্তালাপ চালিয়ে যান। এমনভাবে কেন বসেন, পুরুষদের প্রলুব্ধ করতে? এহেন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন– “আমি সবসময় বড়ো গলা ব্লাউজ পরি। তা ছাড়া আমি একটু মোটাসোটা বলে খুব গরম লাগে।”
ফুলকলি হিজড়াও বাংলাদেশে থাকেন। বিয়ের স্বপ্ন দেখলেও তিনি বাস্তববাদী। উনি জানেন তাঁর বিয়ের স্বপ্ন থাকলেও কোনো পুরুষ কখনোই তাঁকে বিয়ে করবে না। তাঁর বড় কারণ হিজড়ারা কখনোই সন্তান জন্ম দিতে পারে না। সব পুরুষই বাবা হতে চায়। তাই সেক্স ভোগ করি। বিনিময়ে অর্থ নিই। হিজড়া সমাজে থাকলেও নিজের বাড়িতে বাবা-মাকে টাকা পাঠাই। ফুলকলি জানান– “আমি একটি ছেলেকে পছন্দ করতাম। একে অপরকে ভালোবাসতাম। একদিন বিয়ে কথা ভেবে ছেলেটি অভিভাবকদের সঙ্গে কথা তাঁরা জানাল, আমি তো কোনোদিন সন্তান দিতে পারব না। তাহলে কেন ছেলেটার জীবন নষ্ট করব!” জীবন নিয়ে হতাশ ফুলকলি বলেন– “আমার শরীর দেখে কারোর লোভ লাগতেই পারে। কারণ আমার শরীরের মেয়েদের চেয়ে কিছু কম নেই। বাস্তবে তো আমাদের নিয়ে শোয়া আর একটা কলাগাছকে নিয়ে শোয়া একই ব্যাপার। সাধ আছে সাধ্য নেই। আমার ভিতরে আবেগ আছে, বাইরে শরীর আছে। এমন শরীর যা যৌনতা ছাড়া সৃষ্টি করতে পারে না। পুরুষ মানুষদের কাছে আমরা হলাম ‘ওয়ান টাইম ইউজড, টু টাইম ডাস্টবিন। মাঝেমাঝে মনে হয় আমার জীবনে আমি কী পেলাম। মনে হয় গলায় দড়ি দিয়ে মরে যাই। চাই না এই দুনিয়ায় থাকতে। আল্লাপাক যদি আমাকে পরের জন্মে নারী বা পুরুষ হিসাবে জন্ম দিত তাহলে আমি আল্লাহর কাছে অনেক হ্যাপি হতাম। কিন্তু শুনেছি আত্মহত্যা করা মহাপাপ। আমি এভাবে মরব না। ধুকে ধুকে মরব। যত দিন যাবে আমি তিলে তিলে মরব। আমি প্রতিদিন রাত হলে কাঁদি। আল্লাকে বলি, আল্লা তুমি আমাকে নিয়ে যাও।”
তানজিমা বলেন “ছোটোবেলায় ছিলাম একরকম। অর্থাৎ একজন পুরুষ। তাই আমার নাম হয়েছিল নাহিদ। কিন্তু আমি পুরুষ শরীর জন্মালেও আমার মন ছিল একজন নারীর মতো। অর্থাৎ আমি মেয়েদের মতো কাজকাম করতাম। বাড়ির মা-মাসিরা যে ধরনের কাজ করতেন, আমারও সেই কাজ করতে ভালো লাগত। ছোটোবেলায় আমি মেয়েদের মতো পুতুল খেলতাম। মেয়েদের মতো সাজগোজ করতাম। মেয়েদের মতো হাঁটাচলা করতে পছন্দ করতাম। আমার ভালো লাগত। আমার মা বলত– বাবা, এগুলো তোমার কাজ না। এগুলো মেয়েদের কাজ। ছেলেরা যে ধরনের কাজ করে যে ধরনের কাজ করে তুমি সেগুলো করো। কিন্তু আমি অপারগ ছিলাম। আমার বাবা-মা যখন স্কুলে ভর্তি করে দিল, তখন রাস্তায় অনেকে বলত ‘মাইগ্যা হাঁইটা যাচ্ছে। স্কুলে গেলে ছেলেরা বলত, “তুই তো হাফ লেডিজ। মেয়েদের কাছে গিয়ে বস’। মেয়েদের কাছে গিয়ে বসলে মেয়েরা বলত, ‘তুই তো হাফ লেডিজ। ছেলেদের কাছে গিয়ে বস’। আমাকে নিয়ে সবাই হাসি-ঠাট্টা করত। আমার খারাপ লাগত। অনেক মেয়েরা অবশ্য কাছে টেনে নিত। সবাই এরকম বলত না। একদিন রাতে আমার বাবা-মায়ের কয়েকটা কানে এলো। আমার বাবার একটা মুদির দোকান আছে। বাবা মাকে বলছেন, দোকানের লোকেরা এসে বলে ভাই আপনার তো দুটো সন্তান। আপনার বড় ছেলেটা ঠিক আছে। কিন্তু ছোটো ছেলেটা কেমন মেয়েদের মতো। হিজড়াদের মতো চলাফেরা। হিজড়াদের মতো দেখতে। হিজড়াদের মতো কণ্ঠ। এ কথা যখন বাবা মাকে বলছে, তখন দুজনেই কাঁদছিল। আমার বাবা-মায়ের কান্না শুনে আমার খারাপ লেগেছিল। আমি যত বড়ো হচ্ছিলাম আমার ভিতর ততই মেয়েলিপনাটা বেড়ে উঠছিল। আমার প্রতিবেশীরা আমাকে নিয়ে আমার বাবা-মাকে কটুকথা শোনায়। আমার দাদা মামুনকে সবসময় কষ্ট পেত আমার গজন্যে। তাঁর বন্ধুরা বলত, “তোর ভাইকে দেখতে মেয়েদের মতো। তখন আমার দাদা খুব লজ্জা পেত। আমার কাছেও খারাপ লাগত। আজকে আমার জন্যে আমার বাবা-মার চোখে জল। আমার দাদার জন্যে আমার বাবা-মার চোখে জল আসেনি। আমার জন্যে কেন আমার চোখে জল আসবে? হয়তো আমার বাবা-মা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করবে। এটা ভেবে দেখলাম আমার এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া উচিত। তখন ওখানকার মুন্নি নামে হিজড়ার কাছে জানতে পারলাম বর্তমান নান গুরু এনজি হুররামের কথা। শুনেছি উনি খুব ভালো। উনি থার্ড জেন্ডারদের আশ্রয় দেন, তাঁদেরকে বাঁচার জন্য ভালো একটা পথ দেখায়। তখন আমি মুন্নি আপার কাছ থেকে নান গুরুর ফোন নম্বরটা নিয়ে রাখি। পরে যোগাযোগ করে নিই। তিনি আমাকে গ্রহণ করলেন। এক ভোররাতে বাবা মাকে একটা চিঠি লিখে আমি চলে আসি। লিখেছিলাম, ‘আমি চলে গেলাম। ভবিষ্যতে যদি বেঁচে থাকি অবশ্যই কথা হবে দেখা হবে। আমি চাই আমার নান গুরু ওরফে সজীবকে আল্লাহ হাজার বছর বাঁচিয়ে রাখুক। তাঁর মতো একটা মানুষ আমার জীবনটা পুরোটাই চেঞ্জ করে দিয়েছে। সে না-থাকলে হয়তো আমি আজ এ জায়গায় থাকতাম না। সমাজে আমার একটা পরিচয় হয়েছে ভালোভাবে থাকা ভালোভাবে মানুষের সামনে যাওয়া এটা আমার হত না। সে দুই মাস আমাকে কোনো কাজ করতে দেয়নি নিখরচায় আমার ভরণপোষণ করেছে আমার নতুন জামাকাপড় কিনে দিয়েছে। কোনো ভালো জায়গায় গেলে সে আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে। আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার দুই বছর ঢাকা থেকে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলাম। তাঁরা প্রথমে আমাকে চিনতে না পারলও পরে চিনেছে যে আমিই তাঁদের ছোটো সন্তান। কারণ আমার লুকটাই তো বদলে গেছে। বাচ্চা বকসিস ও বিয়েবাড়ি বিনোদন দিয়ে আমি যা রোজগার করি তার একটা অংশ আমার বাবা-মাকে পাঠাই সন্তান হিসাবে।
এবার তানিশা হিজড়ার কথা বলব। তানিশা বাংলাদেশের নাগরিক হলেও সে ভারতে এসে আধুনিক চিকিৎসার সাহায্য নিয়ে স্তনের বৃদ্ধি ঘটিয়েছেন। তানিশ জানিয়েছেন স্তন তাঁর আগে থেকেই ছিল। তবে কিঞ্চিৎ ছোটো থাকায় একটু বড়ো করিয়ে নিয়েছেন আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য। আকর্ষণ বাড়ানোর দুই চোখে লেন্সও পরেন। তানিশা বলেন, “একটা মেয়ে একটা ছেলেকে যতটা সুখ দিতে পারে আমি তাঁদের চেয়ে ১২ গুণ সুখ দিতে পারি।” জন্ম হয়েছিল পুরুষ হিসাবে। তখন নাম ছিল তানবির। নান গুরুর কাছে শিষ্যা হওয়ার পর নাম হয় তানিশা। উনিশ বর্ষীয়া লাজুক তানিশা নিজেকে মেয়ে হিজড়া বলে দাবি করেন। বাংলাদেশ থেকে দিল্লিতে এসে দেড় বছর থেকে তাঁর স্তন তৈরি করান। এই খরচ তিনি সংগ্রহ করেছেন ভারতের এক নাইট ক্লাবে ডান্স করে। কোনো পুরুষের সঙ্গে সংসার করার স্বপ্ন নিয়ে অপেক্ষা করে আছেন। একটা মেয়ে যা দিতে পারবে তার চেয়ে অনেক বেশি দিতে পারবেন বলে দাবি করেন তিনি। কিন্তু বাচ্চা দিতে পারবেন না, এটাই আক্ষেপ।
পুরুষ হিজড়ারা পায়ুকামের (Sodomy) মাধ্যমে যৌনতা করে। দুই সমকামী পুরুষের মধ্যে একজন মেয়েদের মতো Passive বা নিষ্ক্রিয় যৌনসঙ্গী হন। এরা সকলেই পায়ুমিলনে অভ্যস্ত। এই পায়ুপথই (Anal canal) নারীর যৌনাঙ্গের (Vagina) সমতুল মনে করে থার্ড জেন্ডারের মানুষরা। যদিও অনেক কমন জেন্ডার বা বিপরীতকামীদের মধ্যেও পায়ুমৈথুনে অভ্যস্ত। শুধু রোজগারের জন্যই এইসব হিজড়ারা সমকামী কোনো ব্যক্তির সঙ্গে পায়ুমিলনে লিপ্ত হয় না, অবদমিত যৌনক্ষুধাকে তৃপ্ত করার জন্যও এঁরা সমকামে লিপ্ত হয়। মূত্রছিদ্র দিয়ে এক ধরনের রস নিঃসরণের (Urethral Smear) মধ্য দিয়ে এঁদের যৌনসুখের চরম তৃপ্তি বা অর্গাজম অনুভূত হয়।
হিজড়াদের ভোটাধিকার
হিজড়ারা আগেও ভোট দিত, এখনও দেয়। তবে হিজড়া হিসাবে ভোট দেওয়া যায় না। যেহেতু এঁরা নারী-বেশ ধারণ করেন এবং স্ত্রীলিঙ্গে নাম ধারণ করে সেইহেতু ভোটের সময় এঁরা স্ত্রী ভোটার হিসাবেই চিহ্নিত হয়। অথচ রহস্যজনকভাবে এঁরাই আবার জনগণনায় পুরুষ হিসাবে নথিভুক্ত হয়। সর্বভারতীয় হিজড়া কল্যাণ সভার সভাপতি শ্রী খৈরাতিলাল ভোলা হিজড়া ‘হিসাবে’ ভোট দেওয়ার আইনি স্বীকৃতি আদায় করার জন্য ‘Election Commisson of India’-র কাছে আবেদন জানিয়েছেন। আবেদনে সাড়া দিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সমস্ত মুখ্য নির্বাচনী অফিসারের ভোটার তালিকায় হিজড়াদের ‘হিজড়া’ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ পাঠান। সমস্যাটা আর-এক জায়গায়– সমস্ত হিজড়াই নিজেদের ‘স্ত্রীলোক’ হিসাবেই পরিচয় দিতে আগ্রহী। তারা চায় না ভোটার তালিকায় ‘হিজড়া’ হিসাবে নাম থাকুক।
হিজড়াদের সংস্কার
হিজড়া দুনিয়ায় সব সদস্যকেই বেশকিছু নিয়মনীতি মান্য করে চলতে হয়। যেমন –(১) রাস্তায় অপরিচিত কোনো পুরুষের সঙ্গে হালকা চালে কথা বলা এবং অশালীন আচরণ হিজড়াসমাজে গর্হিত অপরাধ। (২) সন্ধ্যার পর হিজড়া মহল্লার সব দরজা বন্ধ হয়ে যায়। অতি পরিচিত কোনো ব্যক্তি ছাড়া ভিতরে প্রবেশ নিযেধ। অবশ্য ঝুপড়িবাসীদের ক্ষেত্রে এই নিয়ম কার্যকর হবে না। (৩) খুব জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বা আমন্ত্রণ না-পেলে কোনো গুরু-মা সাধারণত অপর কোনো গুরু-মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যান না। (৪) কোনো গুরু-মা মাটিতে বসে থাকলে তা চেলা বা শিষ্যরা খাটে বা উঁচু কোনো জায়গায় বসে না। (৫) কিছু কিছু মহল্লায় হিজড়ারা খুব ভোরে উঠে প্রধান দরজার চৌকাঠে ঝাঁটা বা লাঠি দিয়ে আঘাত করে। অনেকে আবার মহল্লার মাথায় ছেঁড়া জুতো বেঁধে রাখে। (৬) হিজড়ারা মনে করে সন্তানসম্ভবা কোনো মহিলার উদর বা পেট যদি কোনো হিজড়া বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করে তাহলে গর্ভস্থ সন্তান হিজড়া হয়ে ভূমিষ্ঠ হবে। (৭) হিজড়ারা মনে করে হিজড়াদের লেখা চিঠি যদি কোনো গর্ভবতী মহিলা পাঠ বা স্পর্শ করে তাহলে ভ্রণের ক্ষতি হবে ইত্যাদি। (৮) তাঁরা বিশ্বাস করে, তাঁরা তাঁদের মৃত্যুর কথা আগাম জানতে পারে। (৯) হিজড়ারা মনে করে তাঁদের গুরু-মা দৈব ক্ষমতার ক্ষমতার অধিকারী। | শিষ্যাদের সম্পর্কে সবকিছুই গুরু-মা জানতে পারেন।
হিজড়াদের ঢোল
হিজড়াদের জীবনে ঢোল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। বাচ্চা নাচাতে ঢোলের বাজনা অত্যাবশ্যক অনুসঙ্গ। কর্মক্ষেত্র ছাড়া অকারণে গুরু-মায়ের সামনে ঢোল বাজালে বা হাতের তালি দিলে শিষ্যদের ক্ষতি হবে বলে বিশ্বাস। হিজড়াদের বিশ্বাস ঢোল পায়ে লাগা পাপ। সকালে, বিকালে ঢোলকে এঁরা প্রণাম করে। কোনো-কোনো মহল্লায় কাজের শেষে ঢোলগুলিকে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় রেখে সিঁদুরের ফোঁটা দেওয়া হয়। সকালে কাজে বেরনোর আগে যদি কোনো অ-হিজড়া ঢোল স্পর্শ করে তাহলে ঢোলটি অপবিত্র হয়ে যায়। সেদিনের জন্য ওই ঢোল বাতিল, অন্য ঢোল নিয়ে কাজে বেরতে হয়। হাজারো বিপদের মাঝে নিজের জান দিয়ে হলেও ঢোলকে অক্ষত রাখা হিজড়াদের অসীম কর্তব্য। হিজড়াদের বিশ্বাস, এই ঢোল যদি অন্য কেউ কেড়ে নেয় তাহলে মনে করা হয় বিপদ নিকটেই। এছাড়া মহল্লার গুরু-মায়ের সম্মতি ছাড়া ঢোল ক্রয় করা গর্হিত অপরাধ। সমস্ত হিজড়া মহল্লার ঢোল পুজো হয়। ঢোল পুজো হিজড়াদের একটি বাৎসরিক উৎসব। কালীপুজোর রাতে এঁরা ঢোলের আরাধনায় বসে। এদিন কেউ কাজে বেরন না। নিরামিষ খাবে সবাই। ঢোল পুজোর অনুষ্ঠানে বাইরের কেউ প্রবেশাধিকার পায় না। পুরোনো চামড়ার | ঢোল এই পুজোর বাতিল। যাই হোক, পুজোয় বসেন গুরু-মা। কোনো নির্ধারিত মন্ত্র-টন্ত্র নেই এই পুজোয়। গুরু-মা চোখ বন্ধ করে ধ্যানে বসে, ধ্যান ভাঙলে পুজো শেষ।
হিজড়াদের ধর্মবিশ্বাস
জাতি-ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়নির্বিশেষে সমস্ত রকমের ভেদাভেদ ভুলে এক সম্প্রীতির সমাজ গড়ে তুলেছে হিজড়া সমাজ। যে-কোনো হিজড়া মহল্লায় দেখা মিলবে সব ধর্মের হিজড়া। পারস্পরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি, সহমর্মিতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এরা ধর্মীয় সহিষ্ণুতা গড়ে তুলেছে। ধর্মের ব্যাপারে কোনো বাড়াবাড়ি বা রক্ষণশীলতা এক্কেবারেই নেই। সব ধর্মের দেব-দেবতাই সকল হিজড়াদের ইষ্টদেবতা।
এঁদের অধিকাংশেরই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান হিন্দু ধর্মের সঙ্গে মেলে। কিন্তু সামাজিক জীবনযাত্রার উপর ইসলামের প্রভাব বিস্তর। হিজড়াদের অধিকাংশ দলপত্নী বা গুরু-মা ইসলাম ধর্মাবলম্বী হন। তামিল লুনার ক্যালেন্ডার মতে নববর্ষের দিন সারা ভারতের হিজড়া সম্প্রদায়ের বার্ষিক অনুষ্ঠান পালিত হয়। মাদ্রাজ থেকে প্রায় ২০০ মাইল দক্ষিণে কোষাগাম গ্রামে তাঁরা একসঙ্গে মিলিত। বাংলাদেশের হিজড়ারাও ভারতে আসেন। তাঁরা মনে করেন ভারতের মানুষের কাছ থেকে হিজড়ারা সম্মান পান। ভারতের মানুষরা হিজড়াদের সমীহ করে।
হিজড়াদের মন ও মনন
নারী না-হয়েও হিজড়ারা নিজেদের নারীরূপে ভেবে থাকে। মহিলাদের পোশাক আশাক, মহিলাদের অলংকার-কসমেটিক-শৃঙ্গার এদের পছন্দ অপ্রতিরোধ্য। ট্রেনে-বাসে লেডিস সিট, লেডিস কম্পার্টমেন্ট, লেডিস ট্রেন, লেডিস বাসে চড়ে বা উঠে যাতায়াত করে। ভুলেও এরা জেনারেল আসন বা কম্পার্টমেন্ট ব্যবহার করে না। শেষ মুহূতে ট্রেনের জেনারেল কম্পার্টমেন্টে উঠে পড়লেও পরের স্টপেজে নেমে লেডিস কম্পার্টমেন্টে ওঠে। পুজোর প্যান্ডেলে বা যাত্রার এঁদের মহিলাদের মধ্যেই দেখা যায়। বস্তুত এঁরা নিজেদেরকে অম্বার জাত বা উত্তরসূরী ভাবে। অম্বা মহাভারতের একটি অভিশপ্ত চরিত্র। গল্পটা একটু বলি; ভাই বিচিত্রবীর্যের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য স্বয়ংবর সভা থেকে ভীষ্ম অম্বাকে হস্তিনাপুরে নিয়ে এলেন। কিন্তু শারাজার প্রতি অনুরাগের কথা শুনে ভীষ্ম অম্বাকে মুক্তি দেন। অপরদিকে শান্বরাজ অম্বাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। এহেন ঘটনার অম্বা জোর গলায় ভীষ্মকে অভিযুক্ত করে। এখানেই শেষ নয়, অম্বা ভীষ্মকে ধ্বংস করবে এমন বিধ্বংসী তপস্যায় ব্রতী হলেন। শিব সন্তুষ্ট হয়ে অম্বাকে বর দিলেন। বললেন– এ জন্মে নয়, পরজন্মে নপুংসক ‘শিখণ্ডী’ হয়ে অম্বা জন্মগ্রহণ করবেন এবং ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ হবে। হিজড়ারা এই কাহিনি জানে, জানে বলেই তারা নিজেদেরকে অম্বার সঙ্গে গভীর একাত্মতা অনুভব করে। হিজড়ারা বিশ্বাস করে তারা নপুংসক শিখণ্ডী– এ জন্মের আগে তাদেরও ছিল স্বাভাবিক জীবন এবং পরের জন্মে আবার নারীজন্ম ফিরে পাবে।
স্বাভাবিক কর্মজীবনে হিজড়াদের ভূমিকা
হিজড়াদের সেই পরিচিত কর্মের বাইরে মূলস্রোতে কর্মরত অবস্থাতেও দেখা যাচ্ছে। কিছু খ্রিস্টান সংঘ হিজড়াদের সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করেন। ইউনিটারিয়ান একটি উদার ধর্মমত। তাদের মূল খ্রিস্টান ধর্মের সঙ্গে যুক্ত। ১৯৭৯ সালে তারাই সর্বপ্রথম হিজড়াদের পূর্ণ সদস্য হিসাবে গ্রহণ করে। and the first to open an Office of Bisexual, Gay, Lesbian, and Transgender Concerns in 1973. ১৯৮৮ সালে উইনিটারিয়ান উইনিভার্সালিস্ট অ্যাসোসিয়েশান প্রথম একজন হিজড়া ব্যক্তিকে মনোনীত করে। ২০০২ সালে শ্যন ডেন্নিসন প্রথম হিজড়া ব্যক্তি যিনি ইউনিটারিয়ান ইউনিভার্সালিস্ট মন্ত্রনালয়ে ডাক পান। ২০০৩ সালে ইউনাইটেড চার্চ অফ খ্রিস্ট সকল হিজড়া ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে মত দেয়। ২০০৫ সালে ট্রান্সজেন্ডার সারাহ জোনস চার্চ অফ ইংল্যান্ডের ধর্মযাজক হিসাবে নিয়োগ পান। ২০০৮ সালে ইউনাইটেড মেথোডিস্ট চার্চ জুডিশিয়াল কাউন্সিল রায় দেন যে ট্রান্সজেন্ডার ড্রিউ ফনিক্স তাঁর পদে বহাল থাকতে পারবেন। ওই একই বছরে মেথোডিস্টদের একটি সাধারণ বৈঠকে একাধিক হিজড়া ক্লারজির বিরুদ্ধে পিটিশন খারিজ করে দেওয়া হয়। ভারতের বিহারে ‘কালী হিজড়া’ পশ্চিম পাটনা কেন্দ্র থেকে ‘জুডিসিয়াল রিফর্মস’ পার্টির প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন। ১৯৯৫ সালে পশ্চিমবাংলার টিটাগড় পৌরভোটে ১৪ নং ওয়ার্ড থেকে ‘হিজড়া’ বৈজয়ন্তীমালা মিশ্র ভোটপ্রার্থী হয়েছিলেন। ১৯৯৬ সালের লোকসভায় মহারাষ্ট্রের জালনা কেন্দ্র থেকে নির্দল হিজড়া প্রার্থী রমেশ ওরফে মালা ভোটপ্রার্থী হয়েছিলেন।
উত্তর চব্বিশ পরগণার নৈহাটির কারখানা শ্রমিক বাবার মধ্যবিত্ত পরিবারে ছেলে হিসেবে জন্ম হয় সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ করে কলকাতার একটি কলেজ থেকে বাংলায় স্নাতক সম্পন্ন করেন তিনি। পড়াশোনা শেষে পশ্চিমবঙ্গের মাওবাদী (ঝাড়গ্রাম) অধ্যুষিত অঞ্চলের এক কলেজে বাংলার শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন তিনি। এ সময়েই নারী ও তৃতীয় লিঙ্গের অধিকারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে লেখালেখি ও সামাজিক আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। পরে ২০০৩ সালে জটিল এক অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নিজেকে নারীতে রূপান্তরিত করেন সোমনাথ, এখন তিনিই মানবী বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫১ বছর বয়সি মানবী বন্দ্যোপাধ্যায় এখন পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ। ২০১৫ সালের ৯ জুন থেকে তিনি নতুন দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। ভারতে প্রথমবারের মতো তৃতীয় লিঙ্গের (হিজড়া) একজনকে কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করা হয়েছে। এটা তৃতীয় লিঙ্গদের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।সম্প্রতি অনেকে নিশ্চয় লক্ষ করেছেন যে, ভারত সরকারের একটি ট্র্যাফিক সংক্রান্ত বিজ্ঞাপন হিজড়াদের দিয়ে করানো হয়েছে। তবে বাংলাদেশে হাসিনা সরকার হিজড়াদেরকে ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণের কাজে লাগানো যায় কি না ভাবছেন।
তবে দৈনিক প্রথম আলোর একটি সংখ্যায় ছাপা হয়েছে, বাংলাদেশের জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ হিজড়া। হিজড়াদের দেওয়া তথ্যমতে বাংলাদেশে এঁদের সংখ্যা প্রায় ১,৫০,০০০। শুধু ঢাকাতেই বসবাস করে ১৫,০০০ হিজড়া। তবে বেশিরভাগই অন্য জেলা থেকে এসেছে রাজধানীতে রুজি-রোজগারের আশায়। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, হিজড়াদের নিয়ে সরকারের কোনো কার্যক্রম নেই। তবে সরকার অপরাপর জনগোষ্ঠীর তথ্য সংগ্রহ করেন। ২০১১ সালের আদমসুমারির রিপোর্টে দেখানো হয়েছে যে, বাংলাদেশে ২৭টি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী আছে। তাঁদের মোট সংখ্যা ১৫,৮৬,১৪১ এবং প্রতিবন্ধী জনসংখ্যা ২০,১৬,৬১২, যা মোট জনসংখ্যার ১.৪ ভাগ। দৈনিক যুগান্তরে এ বিষয়ে রিপোর্ট করা হয়েছে, সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাছে হাজারের নীচে ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর হিসাব আছে, তেমনি আছে প্রতিবন্ধীদেরও আলাদা আলাদা হিসাব। তবে হিজড়াদের কোনো পরিসংখ্যান সরকারের কোনো বিভাগ সংরক্ষণ করে না। ২০০৮ সালে লিঙ্গ নির্ধারণ না করেই প্রথমবারের মতো ভোটাধিকার পায়। তবে ভোটার আইডি কার্ডে লিঙ্গ-পরিচয় না-থাকায় তাঁদের বিড়ম্বনার অন্ত ছিল না। জাতীয় আদমসুমারি ২০১১ সালের মধ্যেও হিজড়াদের গণনা করা হয়নি, এমন অভিযোগ করেছে বাংলাদেশের ‘বাঁধন হিজড়া সংঘ’ এএফপিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে। বাংলাদেশে নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা বেশি হওয়ায় আদমসুমারিতে এঁদের অধিকাংশকেই দেখানো হয় পুরুষ হিজড়া হিসাবে। ফলে এঁদের নিয়ে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই বেশ বিড়ম্বনায় পড়তে হয়। কারণ এঁদেরকে টিক চিহ্ন দিতে হয় পুরুষ কিংবা নারীর ঘরে। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সংগঠন এই স্বীকৃতির দাবি জানিয়ে আসছিল।
অবশেষে ২০১৩ সালে বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পরিষদে উত্থাপিত হিজড়াদের নারী-পুরুষের পাশাপাশি আলদা লিঙ্গ বা তৃতীয় লিঙ্গ হিসাবে স্বীকৃতির বিলটি পাস হয়েছে। স্বীকৃতি পরবর্তী নির্দেশ জারি করা হয় যে, সার্টিফিকেট, ভিসা, বিমা, ব্যাংক সর্বক্ষেত্রে লিঙ্গ নির্ণয়ে তৃতীয় লিঙ্গের অপশন রাখতে হবে এবং তাঁদের পরিচয়ে হিজড়াই লিখতে হবে, অন্য কোনো শব্দ নয়। এ স্বীকৃতি হিজড়াদের জন্যে অবশ্যই মন্দের ভালো। কিন্তু সুপারিশমালায় পরিসংখ্যানে জানানো হয়েছে এঁদের সংখ্যা ১০ হাজার। হিজড়াদের সংগঠন ‘বন্ধু সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি সূত্রে জানা যাহ, সারা দেশে হিজড়ার সংখ্যা ১০ হাজার থেকে ১৫ হাজার। বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থার দাবি, সারা দেশে ৫০ হাজার হিজড়া আছে। ডেমোগ্রাফি সূত্র অনুযায়ী শুধু ঢাকার মধ্যে হিজড়ার সংখ্যা ২৫ হাজারেরও বেশি।
হিজড়াদের মৃত্যু ও সৎকার
সাধারণ মানুষের কাছে এ এক রহস্যজনক অধ্যায়। কোনো রহস্য নেই, সবটাই উন্মোচিত। আমাদের অজ্ঞানতাই এসব জানতে পারি না। এঁদের প্রতি আমাদের চরম অবহেলা আর উদাসীনতাই রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। হিজড়াদের মৃতদেহ কেউ দেখেছে কি না এ প্রশ্ন অনেকসময় শুনতে হয়। উত্তর সবার কাছে নেই, তাই ভ্যাবাচাকা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া তেমন কিছু করারও নেই। বস্তুত হিজড়াদেরও মৃত্যু হয়, মৃতদেহও হয়, মৃতদেহের সৎকারও হয়। মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে হিজড়াদের শবযাত্রাও হয়। তবে তা নিঃশব্দে গভীর রাতে। শ্মশান বা গোরস্থানের কিছুটা আগে মৃতদেহকে দাঁড় করানো হয়। এরপর চতুর্দিক থেকে মৃতদেহকে ঘিরে থাকে হিজড়ারা। তারপর মৃতদেহকে কিছুক্ষণ হাঁটানো হয়। মৃতদেহকে কি হাঁটানো সম্ভব? মোট্টেও সম্ভব নয়। অগত্যা টেনে হিছড়ে নিয়ে আসা হয়। শ্মশান বা গোরস্থানে এসে নির্দিষ্ট জায়গায় শুইয়ে দিয়ে মৃতদেহকে উপর্যুপরি লাথি মারা হয়। লাঠিপেটাও করা হয়। মৃতব্যক্তি যত বড়ো প্রিয় মানুষ হন না-কেন এই আচরণে অন্য হিজড়াদের একদম কাঁদা চলবে না। নিয়ম নেই। হিন্দু হলে নগ্ন করে চিতার উপর শোয়ানো হয়, মুসলমান হলে মাটি দেওয়ার আগে মৃতদেহকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে স্নান করানোর রীতি আছে। তবে পাঞ্জাবের বেশ কিছু জেলায় মৃত্যুর পর বাড়ির ছাত সরিয়ে হিজড়াদের বাইরে বের করে আনা হয়। যাতে ভোলা ছাতের মধ্য দিয়ে মৃতব্যক্তির আত্মা চিরতরে আকাশে বিলীন হয়ে যায়। মৃতব্যক্তি যদি গুরু-মা হন, তবে হিন্দুদের ক্ষেত্রে তাঁর বড় মেয়ে বা শিষ্য বা চেলা মুখাগ্নি করবে। মুসলমান হলে বড়ো মেয়ে বা শিষ্য বা চেলাই পারলৌকিক সমস্ত ক্রিয়াকর্মের সম্পাদনের মূল দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়। এরপর কোথাও দীর্ঘ এক মাস কোথাও-বা ৩৯ দিন ধরে চলে অশৌচ পর্ব। অন্য হিজড়া মহল্লার হিজড়ারও অশৌচ পালন করে, তবে সেটা চারদিনের মাত্র। হয় শ্রাদ্ধানুষ্ঠানও, নিমন্ত্রণ রক্ষা করে হিজড়ারাই।
হিজড়া আর সমকামী কি সমার্থক?
সেই প্রশ্নটাই আবার ঘুরে ফিরে এল। হিজড়া আর সমকামী কি সমার্থক? বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। আদিকাল থেকে সমকাল পর্যন্ত শিল্প-সাহিত্যেও মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত অভিলাষ সমকামিতার প্রতিফলন। অথচ ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আদালতের রায়ে সহস্রাব্দ প্রাচীন সমকাম আজ ‘বিকৃত’ সমকামিতা অপরাধ। গ্রিক সভ্যতা থেকে প্রাচীন ভারত। সমকামিতার উদাহরণ যুগে যুগে। প্রাচীন নাগরিক সমাজ, ব্যক্তির স্বাধীনতা, আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ধারণা যেখানে জন্ম নিয়েছিল গ্রিসে। সেই গ্রিস, যে কখনও নাগরিকের যৌন স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেনি। সমলিঙ্গ যৌন সংসর্গের বৈধতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন ছিল না সেখানে। হেরোডেটাস, প্লেটোর মতো দার্শনিক-চিন্তাবিদদের লেখায় প্রায়ই পাওয়া যায় সমকামী সম্পর্কের কথা। আনুমানিক খ্রিস্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রিসের লেসবস দ্বীপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন স্যাফো। এই মহিলা কবির লেখার প্রতিটি পরতে পরতে নারী শরীরের বন্দনা। স্যাফোর জন্মস্থান লেসবস থেকেই তো অভিধানে জায়গা পেয়েছে লেসবিয়ান শব্দটি। পাশ্চাত্য থেকে এবার আসা যাক প্রাচ্যে। ইতিহাস বলছে, প্রাচীন পারস্যে সমকামী সম্পর্কের প্রচলন ছিল। যেমনটা ছিল, এই ভারতবর্ষেও। বহু হিন্দু মন্দিরের দেওয়ালের ভাস্কর্য তো সমকামেরই অভিজ্ঞান। পুরাণে বিষ্ণুর মোহিনী রূপ আর অর্ধনারীশ্বর শিব, মহাকাব্য- পুরাণের পাতায় পাতায় যেন তৃতীয় লিঙ্গের সদর্প উপস্থিতি। এমনকী, বাৎসায়নের কামসূত্রও বলছে সমকামিতা যৌন সম্পর্কেরই অন্য রূপ।
সমকামিতা বলতে আমরা সাধারণ অর্থে বুঝি পুরুষের সঙ্গে পুরুষের বা নারীর সঙ্গে নারীর যৌন সম্পর্ক। সমকামিতা কিন্তু যৌন সম্পর্কের উপর নির্ভর করে না, এটা নির্ভর করে যৌন আকর্ষণের উপরে। একটি ছেলে কোনোদিন যৌন সম্পর্ক করেনি, কিন্তু করলে সে একটি মেয়েকেই বেছে নেবে। সে মেয়েদের প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করে বা প্রেমে পড়ে। ছেলেটি যদি ঠিক তেমন আকর্ষণ একটি ছেলের প্রতি অনুভব করে বা ছেলে হয়ে ছেলের প্রেমে পড়ে তখন সে সমকামী। যৌন সম্পর্ক হোক বা না-হোক। মোদ্দা কথা হল— সমকামিতা একটা পছন্দ, কাজ নয়। স্বাভাবিক যৌন আকর্ষণ সম্পন্ন ব্যক্তিকে, অর্থাৎ একজন নারী একজন পুরুষকে অথবা একজন পুরুষ একজন নারীর প্রতি যৌন-আকর্যণ বোধ করলে, তাকে স্ট্রেইট (Straight) বলা হয়। সমকামিতা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ধারণা আছে। এ সংক্ষেপে শ্রেণিবিভাগগুলি আলোচনা করে নিতে পারি বোঝার জন্য। এই শ্রেণিবিভাগ করে হয়েছে একজন নিজেকে কী মনে করে ও কী পছন্দ করে তার উপর ভিত্তি করে।
(১) গে (Gay) : একজন পুরুষ নিজেকে পুরুষ মনে করে। পুরুষের পোশাক পরে এবং একজন পুরুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। এই ধরনের দুইজন পুরুষ বিয়ে করলে এদের মধ্যে স্বামীকে ‘টপ’ এবং স্ত্রীকে ‘বটম’ বলে।
(২) লেসবিয়ান (Lesbian) : একজন মেয়ে নিজেকে মেয়ে মনে করে। মেয়েদের পোশাক পরে এবং একজন মেয়ের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। এই ধরনের দুইজন মেয়ে বিয়ে করলে এরা পুরুষালি পোশাকে ও আচরণে একজন স্বামীর ভুমিকা পালন করে।
(৩) ট্র্যানিঃ একজন পুরুষ সে নিজেকে মেয়ে মনে করে। অপরদিকে একজন মেয়ে, সে নিজেকে পুরুষ মনে করে। সে মনে করে সে ভুল দেহে জন্মেছে। এঁরা বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পড়ে। অনেকে হরমোন প্রয়োগ ও অস্ত্রপচার করে শরীরের পরিবর্তন করে বিপরীত লিঙ্গের হওয়ার চেষ্টা করে। মোদ্দা কথা এদের শরীর এক লিঙ্গের, কিন্তু মন আর-এক লিঙ্গের। যে-কোনো লিঙ্গের প্রতি এঁদের আকর্ষণ থাকতে পারে। তবে বেশির ভাগ হিজরা এই “ট্রানি’ ক্যাটাগরিতে পড়ে।
(৪) বাই (Bisexuality) : একটি ছেলে বা একটি মেয়ে, সে অপর কোনো ছেলে বা মেয়ে উভয়ের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। একটি ছেলে যে মেয়েদের প্রেমেও পড়ে আবার ছেলেদের প্রেমেও পড়ে, যৌনকর্ম করতে সমর্থ। সানি লিওনও এজন বাইসেক্সচুয়াল পর্নস্টার।
সমকামিতা (Homosexuality) একটি যৌন অভিমুখিতা, যার দ্বারা সমলিঙ্গের ব্যক্তির প্রতি যৌন আকর্ষণ বোঝার। এইরূপ আকর্ষণের কারণে এক লিঙ্গের মানুষের মধ্যে যৌন-সম্পর্ক ঘটতে পারে। প্রবৃত্তি হিসাবে সমকামিতা বলতে বোঝায় মূলত সমলিঙ্গের ব্যক্তির প্রতি স্নেহ বা প্রণয়ঘটিত এক ধরনের যৌন প্রবণতা। এই ধরনের সম্পর্কের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ব্যক্তিগত বা সামাজিক পরিচিতি, এই ধরনের আচরণ এবং সমজাতীয় ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত কোনো সম্প্রদায়কেও এই শব্দটি দ্বারা নির্দেশ করা হয়।
উভকামিতা ও বিপরীতকামিতার সাথে সমকামিতা বিপরীতকামী-সমকামী অনবচ্ছেদের অন্তর্গত যৌন অভিমুখিতার তিনটি প্রধান ভাগের অন্যতম বলে স্বীকৃত। ব্যক্তির মনে কেমন করে কোনো নির্দিষ্ট যৌন অভিমুখিতার সঞ্চার হয় সেই ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ নেই। অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন জিনগত, হরমোনগত এবং পরিবেশগত কারণ একত্রে যৌন অভিমুখিতা নির্ধারণের জন্য দায়ী। জীববিদ্যানির্ভর কারণগুলিকে বেশি সমর্থন করা হয়। এর অন্তর্গত হল জিন, জ্বণের ক্রমপরিণতি, এই দুই প্রভাবের মেলবন্ধন অথবা এই সব কিছুর সঙ্গে সামাজিক প্রভাবের মেলবন্ধন। যৌন-অভিমুখিতা নির্ধারণে যে সন্তানপালন বা শৈশবের অভিজ্ঞতার কোনো ভূমিকা আছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। সমলিঙ্গের প্রতি যৌন আচরণের প্রভাবক হিসাবে এক পরিবেশে থাকার ভূমিকা মহিলাদের ক্ষেত্রে নগণ্য এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে শূন্য। কেউ কেউ সমকামী যৌনাচরণকে অপ্রাকৃতিক মনে করলেও বৈজ্ঞানিক গবেষণা থেকে জানা গেছে সমকামিতা মানব যৌনতার একটি সাধারণ ও প্রাকৃতিক প্রকার মাত্র এবং অন্য কোনো প্রভাবকের অস্তিত্ব ছাড়া এটি মনের উপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলে না। অধিকাংশ মানুষের অভিজ্ঞতায় যৌনতার ব্যাপারে সচেতন পছন্দের কোনো ভূমিকা থাকে না। যৌন অভিমুখিতা পরিবর্তনের বিভিন্ন কর্মসূচির কার্যকারিতা সম্পর্কে যথেষ্ট প্রমাণ নেই।
একজন সন্তান সে নারী হবে না পুরুষ হবে, সে মুখ্য ভূমিকা পালন করে হরমোন। শরীরের ভিতর সব কারসাজি করে টেস্টোস্টেরন ও ইস্ট্রোজেন হরমোন। অর্থাৎ মানুষের নারী হওয়ার জন্য দায়ী ইস্ট্রোজেন হরমোন এবং পুরুষ হওয়ার জন্য দায়ী টেস্টোস্টেরন হরমোন। এবার একটু দেখে নিই এই হরমোন কীভাবে কাজ করে বা প্রতারণা করে।
টেস্টোস্টেরন : টেস্টোস্টেরন পুরুষত্বের জন্য দায়ী প্রধান স্টেরয়েড হরমোন যা এন্ড্রোজেন গ্রুপের। মানুষ সহ সকল স্তন্যপায়ী, পাখি, সরীসৃপ প্রাণীর শুক্রাশয়ে এটি উৎপন্ন হয়। স্তন্যপায়ী প্রাণীর ক্ষেত্রে পুরুষের শুক্রাশয় এবং নারীর ডিম্বাশয় থেকে উৎপন্ন হয়, যদিও স্বল্প পরিমাণ অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি থেকে ক্ষরিত হয়। এটি প্রধান পুরুষ হরমোন, যা শুক্রাশয়ের লিডিগ কোশ (Leydig Cell) থেকে উৎপন্ন হয়। পুরুষের জন্য টেস্টোস্টেরন প্রজনন অঙ্গ যেমন শুক্রাশয় (Testis) বর্ধনের পাশাপাশি গৌণ বৈশিষ্ট্য যেমন মাংসপেশি, শরীরের লোম বৃদ্ধি করে। পুরুষদের মাঝে টেস্টোস্টেরন বিপাক হার নারীদের তুলনায় ২০ গুণ বেশি। সাধারণত এন্ড্রোজেন প্রোটিন সংশ্লেষণ করে এবং এন্ড্রোজেন রিসেপ্টর সংবলিত টিস্যুর বৃদ্ধি সাধন করে। টেস্টোস্টেরনের প্রভাবকে লৈঙ্গিক (virilizing) এবং অ্যানাবলিক (Anabolic) এই দু-ভাগে ভাগ করা যায়।
মাংসপেশি বৃদ্ধি, হাড়ের ঘনত্ব (density) বৃদ্ধি, হাড়ের পূর্ণতা প্রাপ্তিতে উদ্দীপনা করা এসব অ্যানাবলিক কাজ। যৌন অঙ্গের পূর্ণতা প্রদান করা, বিশেষ করে ফিটাসের শিশ্ন এবং শুক্রথলি তৈরি এবং জন্মের পরে (বয়ঃসন্ধিকালে) কণ্ঠস্বর গাঢ় হওয়া, দাড়ি এবং বগলের চুল বৃদ্ধি এসব এন্ড্রোজেনিক কাজ। এসবের অনেক কিছুই পুরুষের সেকেন্ডারি যৌন বৈশিষ্ট্য। শৈশবের পরে এন্ড্রোজেন লেভেল বৃদ্ধির লক্ষণীয় প্রভাব দেখা যায় ছেলে এবং মেয়ে উভয়েরই। যেমন– বয়স্ক-টাইপ শরীরের গন্ধ, বগল ও শ্রোণীদেশে চুল গজায়, উচ্চতায় বৃদ্ধি, গোঁফ ও দাড়ি গজানো, পুরুষালী কণ্ঠস্বর হয়।
প্রাপ্তবয়স্ক নারীর এন্ড্রোজেনের মাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশি হলে বয়ঃসন্ধিকালীন প্রভাব দেখা যায়। ছেলেদের এই প্রভাব সচরাচর একটু দেরিতে হয়, কিন্তু মেয়েদের রক্তে মুক্ত টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ অনেক দিন থেকে বেশি মাত্রায় থাকলে এমনটি দেখা যায়। সিবেসিয়াস গ্রন্থি বেড়ে যাওয়া। এটি ব্রণের কারণ হতে পারে। ভগাংকুর (Clitoris) বর্ধিত হওয়া। শ্রোণীদেশের চুল নিচে উরু এবং উপরে নাভী পর্যন্ত বিস্তৃত। মুখমণ্ডলে চুল (জুল্পি, গোঁফ, দাঁড়ি)। মাথার চুল কমে যাওয়া, বুকে, বৃন্তের চারপাশে, নিতম্বের চারপাশে লোম, পায়ে পশম বা লোম, বগলে চুল, মুখের উপরস্থ ফ্যাট কমে যাওয়া, পেশি বৃদ্ধি, গাঢ় কণ্ঠস্বর, পুরুষের উর্বরতা বৃদ্ধি, কাঁধ প্রসারিত, বুকের পাঁজর ফুলে যাওয়া, হাড়ের পূর্ণতা প্রাপ্তি এবং বৃদ্ধি রোহিত হওয়া।
টেস্টোস্টেরনের প্রভাব বয়স্ক নারীর তুলনায় বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে আরও পরিষ্কারভাবে প্রমাণযোগ্য, কিন্তু উভয়ের জন্যই দরকারি। টেস্টোস্টেরনের মাত্রা প্রাপ্তবয়স্ক জীবনের পরে হ্রাস পাওয়ায় এইসবের কিছু প্রভাব প্রত্যাখ্যান করা হতে পারে। স্বাভাবিক শুক্রাণু উৎপাদনের জন্য টেস্টোস্টেরন ভুমিকা রাখে। এটি সারটলি কোশ জিনকে সক্রিয় করে। শারীরিক শক্তি নিয়ন্ত্রক। পেশি গঠন করে। টেস্টোস্টেরন মেগাক্যারিওসাইট ও অণুচক্রিকার থ্রম্বোক্সেন A2 রিসেপ্টরের উপর কাজ করে অণুচক্রিকা একত্রীকরণে ভূমিকা রাখে। টেস্টোস্টেরনের অধিক মাত্রা একই ব্যক্তির যৌন ক্রিয়ার সময়সীমার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু বিভিন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে টেস্টোস্টেরনের মাত্রা কম যৌন সক্রিয় ব্যক্তিদের জন্য বেশি। একাধিক ব্যক্তিদের সঙ্গে যৌন ক্রিয়ায় লিপ্ত ব্যক্তি পরের দিন সকালে টেস্টোস্টেরনের অধিক মাত্রা অনুভব করে থাকেন।
যেসব পুরুষ যৌনতাপূর্ণ সিনেমা ( যেমন– পর্নোগ্রাফি ) দেখেন, তাঁদের টেস্টোস্টেরনের মাত্রা গড়ে ৩৫ শতাংশ বেড়ে যায়, ফিল্ম শেষ হওয়ার পর ৬০-৯০ মিনিটে চূড়ান্তে ওঠে, কিন্তু কোনো বৃদ্ধি যৌন নিরপেক্ষ ছবি দেখার পর হয় না। এছাড়াও যেসব পুরুষ যৌনতাপূর্ণ সিনেমা দেখেন, তাঁদের মানসিক অবসাদ কমে বলে জানা গেছে। আগের গবেষণা যৌন উদ্দীপনা এবং টেস্টোস্টেরনের মাত্রার মাঝে সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছে। ২০০২ সালে একটি গবেষণায় দেখা যায়, একজন মহিলার সঙ্গে সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের পরে পুরুষের মধ্যে টেস্টোস্টেরনের মাত্রা বাড়ে। পুরুষেরা নারীদের মুগ্ধ (Impress) করার চেষ্টা করেছিল। নারীদের দেহের হরমোন চক্রের উপর পুরুষের টেস্টোস্টেরন মাত্রা এবং যৌন উদ্দীপনা বহুলাংশে জ্ঞাত।
ইস্ট্রোজেন : ইস্ট্রোজেন হল প্রাথমিক নারী লৈঙ্গিক হরমোন (primary female sex hormone)। ইস্ট্রোজেনকে বলা হয় নারী হরমোন’। নারী ও পুরুষ উভয়ের শরীরেই এই হরমোন থাকলেও নারীদের প্রজনন বয়সে এটি উচ্চমাত্রায় থাকে। নারী শরীরের সেকেন্ডারি যৌন বৈশিষ্ট্য বিকাশে সাহায্য করে ইস্ট্রোজেন হরমোন। নারীর বাহুমূলের পশম, স্তনের আকার বা গঠন এবং ঋতুস্রাবের মতো শারীরিক বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি এটি প্রজননতন্ত্র গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করে। যদিও ইস্ট্রোজেন পুরুষ এবং নারী উভয়ের মাঝেই থাকে, কিন্তু সচরাচর নারীদের প্রজনন বয়সে এর মাত্রা উচ্চ থাকে। এটি নারীদের সেকেন্ডারি যৌন বৈশিষ্ট্য যেমন স্তন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে এবং একই সঙ্গে মাসিক চক্রের সময় এন্ডোমেট্রিয়ামের পুরুত্ব বেড়ে যায়। শুক্রাণুর পূর্ণতা প্রাপ্তিতে ইস্ট্রোজেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এর পাশাপাশি ইস্ট্রোজেনের আরও কিছু কাজ আছে। যেমন— নারীদের সেকেন্ডারি যৌন বৈশিষ্ট্য উন্নীত করে, বিপাক হার বাড়ায়, ফ্যাট বাড়ায়, এন্ডোমেট্রিয়ামের পুরুত্ব বৃদ্ধি করে, জরায়ুর আকার বৃদ্ধি করে, যোনি পিচ্ছিল করে, জরায়ুর প্রাচীরের পুরুত্ব বৃদ্ধি করে।
সাধারণত একজন মানুষ শিশুর পুরুষালি ও নারীত্ব প্রকাশ পায় না একজন শিশু ধীরে ধীরে বড়ো হয়। কেউ পুরুষ হয়ে ওঠে, কেউ নারী হয়ে ওঠে। বয়ঃসন্ধিতে পূর্ণ বিকাশ হয়। ব্যতিক্রম ক্ষেত্রে একজন শিশু পুরুষ বা নারী হয়ে জন্মালেও কারোর কারোর ক্ষেত্রে হরমোনের কারসাজিতে পুরুষ শরীরে নারীত্ব প্রকট হয় এবং নারীর শরীরে পুরুষালি প্রকট হয় প্রাকৃতিকভাবেই। এঁরাই হিজড়া বা সমকামী বলে পরিচিত হয়। তৃতীয় লিঙ্গ বা থার্ড জেন্ডার হিসাবে বেঁচে থাকে বাকি জীবন। এঁরা সন্তানের জন্ম দিতে পারে না।
সমকামীদের আইনি নিরাপত্তা ও স্বীকৃতি
নানা কারণে স্বঘোষিত সমকামীর সংখ্যা এবং মোট জনসংখ্যার মধ্যে সমলৈঙ্গিক সম্পর্কে আবদ্ধ মানুষের অনুপাত নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এই কারণগুলোর মধ্যে প্রধান হল সমকামভীতিজনিত বৈষম্যের কারণে অনেক সমকামী প্রকাশ্যে তাঁদের যৌনতা স্বীকার না করা। অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যেও সমকামী আচরণের নিদর্শন নথিভুক্ত হয়েছে। অনেক সমকামী মানুষ স্থায়ী পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ আছেন, যদিও আদমশুমারির ফর্ম, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ইত্যাদির আনুকূল্যে তাঁদের আত্মপ্রকাশের পথ নিরাপদ হয়েছে একেবারে সাম্প্রতিক কালে। মূল মনস্তাত্ত্বিক গঠনের দিক দিয়ে এই সম্পর্কগুলি বিপরীতকামী সম্পর্কের সমান। নথিভুক্ত ইতিহাস জুড়ে সমকামী সম্পর্ক এবং কার্যকলাপের প্রশস্তি ও নিন্দা— উভয়েরই নিদর্শন মেলে, কেবল প্রকাশের ভঙ্গিমা ও সংশ্লিষ্ট সংস্কৃতিজনিত তারতম্য দেখা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে সমকামীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বিশ্বব্যাপী আন্দোলন শুরু হয়েছে, যার অন্তর্গত বিবাহ, দত্তক গ্রহণ ও সন্তানপালন, কর্মক্ষেত্রে সমানাধিকার, সামরিক পরিসেবা, স্বাস্থ্য পরিষেবায় সমানাধিকার এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক সমকামীদের নিরাপত্তার স্বার্থে অ্যান্টি-বুলিং আইন। বর্তমানে হোমোসেক্সয়াল শব্দটি বিদ্বৎসমাজে এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হলেও ‘গে’ এবং লেসবিয়ান’ শব্দদুটি অধিক জনপ্রিয়। গে’ শব্দটির দ্বারা পুরুষ সমকামীদের বোঝানো হয় এবং নারী সমকামীদেরকে বোঝানো হয় লেসবিয়ান’ শব্দটির দ্বারা। পশ্চিমে ‘গে’ শব্দটি সমকামী অর্থে প্রথম ব্যবহৃত হতে দেখা যায় সম্ভবত ১৯২০ সালে। তবে সে সময় এটির ব্যবহার একেবারেই সমকামীদের নিজস্ব গোত্রভুক্ত ছিল। মুদ্রিত প্রকাশনায় শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হতে দেখা যায় ১৯৪৭ সালে। লিসা বেন নামে এক হলিউড সেক্রেটারি “Vice Versa: America’s Gayest Magazine” নামের একটি পত্রিকা প্রকাশের সময় সমকামিতার প্রতিশব্দ হিসেবে ‘গে’ শব্দটি ব্যবহার করেন।
বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সমকামী দেশ হল অস্ট্রেলিয়া। এদেশে সমকামীদের অধিকার রক্ষায় কড়া আইন আছে। এখানকার সমকামীদের কেউ কটুক্তি করলে সোজা শ্রীঘর। ইউরোপ-আমেরিকাতে সমকামিতা থাকলেও অস্ট্রেলিয়ার মতো এতটা অধিকার তারা পায় না। সমগ্র পৃথিবীতে থেকে অনেক সমকামী প্রতি বছর স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য অস্ট্রেলিয়ায় আসে। নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্যও সমকামীরা বিশেষ অগ্রাধিকার পায় এদেশে। প্রতি বছর মার্চ মাসে অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মতো ব্যয়বহুল অনুষ্ঠানে সমকামী অর্ধনগ্ন রেলি হয় রাস্তায়। আইনের ভয়ে সমকামিতাকে খারাপ বলার সাহস হয় না কারোর। এখানকার মা-বাবা প্রার্থনা করে যেন তাঁর সন্তান সমকামী না-হয়। অবশ্য সব দেশের বাবা-মায়েরা চান না তাঁর সমকামী বা হিজড়া সন্তান জন্ম নিক। যাই হোক, সমকামী হয়ে গেলে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা এদেশের আইন তাঁদের দেয়নি। অলিম্পিকের আয়োজক দেশ যেভাবে প্রচুর টাকা আয় করে, ঠিক তেমনি অস্ট্রেলিয়া প্রতি বছর প্রায় একই পরিমাণ টাকা সমকামিতাদের সমর্থন করে আয় করে। সমকামী বার, সমকামী ক্লাব, সমকামী রেলি, প্রতি বছর কয়েক হাজার ধনী সমকামী স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য তাঁদের নিজেদের দেশের সমস্ত সম্পদ নিয়ে অস্ট্রেলিয়াতে চলে আসে। সমকামিতা এই দেশের সরকারের বড়ো এক আয়ের উৎস। অনেকে মনে করেন যে কয়টি দেশে সমকামিতা বৈধ, সব দেশেই ব্যাবসার জন্য সমকামিতা বৈধ করা হয়েছে। অস্ট্রেলিয়াতে দামি গাড়ি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমকামীদের কাছেই দেখা যায়। উন্নত বিশ্বে ধনী লোকেরা সমকামী হওয়াতে মিডিয়া, বুদ্ধিজীবি, চিকিৎসক, বিখ্যাত ব্যক্তি এমনকি সরকারও তাঁদেরকে মানসিক রোগী’ বা ‘ফ্যান্টাসি বাতিক’ বলতে পারছে না। বরং তাঁদের এই সমকামিতাকে সমর্থন করলে বিরাট ব্যাবসায়িক লাভ আছে।
অবশ্য কেউ কেউ মনে করেন, ভোগবাদে সমকামিতা একটি পণ্য, অপরদিকে পশুপাখির আচরণের ধারাবাহিকতায় বিরাজমান একটি শখ! ১৩০টির মতো পাখির মধ্যে (এর মধ্যে লেইসান আলবাট্রসের ৩১ শতাংশের মধ্যে মেয়ে-মেয়ে ও গ্রেলাগ গিজের ২০ শতাংশের মধ্যে ছেলে-ছেলে) সমকামিতার প্রধান কারণ প্যারেন্টিংয়ের চাহিদা কম থাকা। পরিবার ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধহীনতা বা এককথায় অসামাজিকতা সমকামিতাকে শখে পরিণত করে। যুক্তরাজ্যের এক্সটার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইভলুশনারি জেনেটিসিস্ট অ্যালান মর মানুষের সমকামিতাকেও সেভাবেই দেখেছেন। ইস্টার্ন সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনে প্রকাশিত ‘Federal distortion of the homosexual footprint’-এ ড: পল ক্যামেরুন দেখিয়েছেন পুরুষ ও মেয়ের বিবাহ-সম্পর্ক আয়ুষ্কাল বাড়িয়ে দেয়, যেখানে সমকামীদের ক্ষেত্রে আয়ুষ্কাল ২৪ বছর কম। পল ক্যামেরুন ব্রিটিশ মেডিক্যাল জার্নাল, কানাডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন জার্নাল, পোস্ট-গ্রাজুয়েট মেডিক্যাল জার্নালের সম্পাদনা করে থাকেন। তাঁর নিজের ৪০টির মতো আর্টিকেল আছে সমকামিতার উপর। ১৯৯০ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে ডেনমাকর্কে স্বাভাবিক যৌনাচারীর গড় আয়ু যেখানে পাওয়া গেছে ৭৪, সেখানে ৫৬১ গে পার্টনার এর গড় আয়ু পাওয়া যায় ৫১! সমকামী মহিলাদের ক্ষেত্রেও এই গড় আয়ুর হার কম, আনুমানিক ২০ বছরের কম! অপরদিকে ধুমপায়ীদের ক্ষেত্রে এই আয়ুষ্কাল কমে যাওয়ার হার মাত্র ১ থেকে ৭ বছর!
১৯৭৩ সালের আগে পর্যন্ত একে ‘মানসিক অসুস্থতা’ হিসাবেই দেখা হত। পরে অবশ্য ১৯৭৩ সালে আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন সমকামিতাকে মানসিক অসুস্থতা থেকে অব্যহতি দেয়। অনেকে মনে করেন সমকামিতা একটি অত্যাধিক ভোগবাদিতার উপকরণ। তা ছাড়া পরিস্থিতিও এর বিকাশ ও পরিপুষ্ট হওয়ার জন্য দায়ী। স্বাভাবিক যৌনসম্ভোগের উপায় না-থাকলে সমকামিতা হয়ে উঠে অপরিহার্য যৌনাচার। সেজন্যই সৈনিকদের মধ্যে এর প্রাদুর্ভাব লক্ষ করার মতো। ULCA-এর আইন স্কুলের উইলিয়াম ইনস্টিটিউটের গবেষণালব্ধ ফলাফলে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীতে আনুমানিক ৬৬,০০০ সমকামী ও উভকামী আছে। ২০০৯ সালের গ্যালপ জরিপেও জানা যায় যুক্তরাষ্ট্রের ৬৯ শতাংশ মানুষ সমকামীদের সেনাবাহিনীতে কাজ করাকে সমর্থন করে। ইংল্যান্ডের লিভারপুল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানী রবিন ডানবার মনে করেন, যুদ্ধ ও শিকারে সমকামিতা পুরুষ গোত্রকে সংগঠিত রাখতে সাহায্য করে। প্রাচীন গ্রিসে স্পার্টানদের এলিট সৈন্যদের মধ্যে সমকামিতাকে উৎসাহিত করা হত। গ্রিক স্পার্টান ছাড়াও অন্য থেবেস, এথেন্সেও সমকামিতার উদাহরণ পাওয়া যায়।
সেক্স বিষয়টি পুরোপুরি শরীরের উপর নির্ভরশীল, কিন্তু জেন্ডার নির্ভরশীল সমাজের উপর। যেহেতু নারী বা পুরুষের দায়িত্ব, কাজ ও আচরণ মোটামুটি সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত হয়, তাই সমাজ পরিবর্তন বা সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জেন্ডার ধারণা বদলে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, আমরা যখন কারোকে ‘নারী’ বা ‘পুরুষ’ হিসাবে চিহ্নিত করি তখন সেখানে জৈবলিঙ্গ নির্দেশ করাটাই মূল উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু মেয়েলি’ বা ‘পুরুষালি’ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহারের মাধ্যমে জেন্ডার প্রপঞ্চকে যুক্ত করা হয় যেখানে, সেখানে নারী বা পুরুষের লিঙ্গীয় বৈশিষ্ট্যকে ছাপিয়ে স্বভাব-আচরণগত ইত্যাদি বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। আর এই কারণেই সেক্সকে জৈবলিঙ্গ এবং জেন্ডারকে সামাজিক বা সাংস্কৃতিক লিঙ্গ বলে অনেকে অভিহিত করেন।
বিপরীতকামী-সমকামী অনবচ্ছেদ অনুসারে যৌন অভিমুখিতার প্রধান তিনটি বর্গের অন্যতম হল সমকামিতা (অপর বর্গদুটি হল উভকামিতা ও বিপরীতকামিতা)। বিভিন্ন কারণে গবেষকেরা সমকামী রূপে চিহ্নিত ব্যক্তির সংখ্যা বা সমলৈঙ্গিক যৌন সম্পর্কে অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের অনুপাত নির্ধারণ করতে সক্ষম হননি। আধুনিক পাশ্চাত্য জগতে বিভিন্ন প্রধান গবেষণার ফলে অনুমিত হয় সমকামী বা সমলৈঙ্গিক প্রণয় ও রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা মোট জনসংখ্যার ২ শতাংশ থেকে ১৩ শতাংশ। ২০০৬ সালের একটি গবেষণায় দেখা যায়, জনসংখ্যার ২০ শতাংশ নাম প্রকাশ না-করে নিজেদের মধ্যে সমকামী অনুভূতির কথা স্বীকার করেছেন। যদিও এই গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে খুব অল্পজনই নিজেদের সরাসরি সমকামীরূপে চিহ্নিত করেন।
পথেঘাটে বা গণিকাপল্লিতে বা বিভিন্ন জায়গায় প্রচুর পুরুষ যৌনকর্মীদের দেখা মেলে। এই পুরুষ যৌনকর্মীরা বেশিরভাগই হয় রূপান্তকামী, না-হয় সমকামী। এঁদের মানসিকতা কিন্তু আলাদা। যৌন-অনুভূতিও আলাদা। পুরুষের খোলস ছেড়ে যাঁদের পরিপূর্ণ নারীতে রূপান্তরিত হওয়ার বাসনা জাগে, তাঁরাই রূপান্তরকামী বা যৌন পরিবর্তনকামী ( Transsexual)। নারীরাও এই ধরনের মানসিকতার হতে পারে। অর্থাৎ নারীর খোলস ছেড়ে পরিপূর্ণ পুরুষে রূপান্তরিত হওয়ার বাসনা জাগে। এঁরা লিঙ্গ ছেদন করতে চায় না। রূপান্তরকামীদের পাশাপাশি আছে সমকামিতা বা Homosexuality। এই দুই মানসিকতার মধ্যে মিল যেমন আছে, তেমনি অমিলও প্রচুর। সব রূপান্তরকামীই সমকামী, কিন্তু সব সমকামীরাই রূপান্তরকামী নয়। সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ থাকলেও সমকামীরা বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরিধান করে না। সমকামী সম্পর্কে আবদ্ধ দুই সম ব্যক্তি একজন পুরুষের মতো সক্রিয় (Active), অপরজন নারীদের মতো নিষ্ক্রিয় (Passive) ভূমিকা পালন করে, যৌনমিলনের ক্ষেত্রে। যদিও বিষমকামীদের ক্ষেত্রে নারীরা কখনো-সখনো যৌনমিলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে, তা সত্ত্বেও সমকামীদের যৌন-ভূমিকাটা বোঝানোর জন্য সক্রিয়-নিষ্ক্রিয় প্রসঙ্গটা উঠে এসেছে। রূপান্তকামিতা এবং সমকামিতা– এই দুই ধরনের মানসিকতা যে শুধুমাত্র শৈশব ও কৈশোরেই দেখা দেবে এমন নয়, পরিণত বয়সেও ধীরে ধীরে সমকামী মানসিকতার জন্ম নিতে পারে।
পর্ন ছবিতে রূপান্তরকামীদের প্রচুর পরিমাণে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। এঁদের যেমন সতেজ এবং প্রমাণ মাপের লিঙ্গ আছে, তেমনি স্বাভাবিক নারীদের চাইতে বেশি সুডৌল-নিটোল স্তনও থাকে। এঁরা টু ইন ওয়ান। অর্থাৎ এঁরা কখনো পুরুষের ভূমিকা নিয়ে পুরুষের পায়ুপথে লিঙ্গ প্রবেশ ঘটায়, কখনোবা নারী হয়ে অন্য পুরুষের লিঙ্গ পায়ুপথে গ্রহণ করে। পর্ন ছবিতে এইসব ‘Shemale’ বা ‘Ladyboy’-দের দাপট লক্ষ করার মতো।
হিজড়াদের মধ্যে যাঁরা যৌনকর্মী তাঁদের ‘ধুরানি’ বলা হয়। হিজড়া সমাজে ‘ধুরানি’ বলতে ‘নারী যৌনকর্মীকেই বোঝায়। যাই হোক, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মর্যাদা অনুসারে ধুরানিদের চারভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—
(১) খানদান ধুরানি (অত্যন্ত ধনী পরিবারের রূপান্তরকামীও সমকামী পুরুষরা খানদান ধুরানি হয়ে আছে। পুরুষের সান্নিধ্য ও যৌনসুখের আকর্ষণেই এঁরা এই পথে আসে)।
(২) লহরি ধুরানি (এরা সাধারণত মধ্যবিত্ত পরিবার থেকেই আসে। এরা যৌন পরিবর্তনকামী পুরুষ। পুরুষ সঙ্গলাভের আশায় এরাও এই পেশা গ্রহণ করেছে।)।
(৩) আদত ধুরানি (আদত ধুরানি হল সমকামী পুরুষ যৌনকর্মীদের একেবারে তলানি। খোলা আকাশের নীচে পলিথিন বিছিয়ে এঁরা খরিদ্দারদের তৃপ্ত করে।)।
(৪) আকুয়া ধুরানি ( স্বেচ্ছায় পুরুষাঙ্গ কর্তন করে হিজড়া সেজেছে এঁরা। এঁরা যৌন পরিবর্তনকামী।)। এঁরা সকলেই সমকাম করে। আসলে হিজড়া দলের একটা বড়ো অংশই হল হয় রূপান্তরকামী, নয় সমকামী। এঁরা পায়ুকামের (Anal Sex) মাধ্যমেই যৌনক্রিয়া করে। তবে পায়ুমৈথুন ছাড়াও মুখমেহন (Oral Sex) এবং সঙ্গীর উরুদ্বয়ে লিঙ্গস্থাপন (Irtra Crusal Sex) করেও যৌনসঙ্গম করে।
ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারায় পায়ুধর্ষণের (Anal Rape) কোনো কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু ৩৭৭ ধারায় পায়ুকামের কথা উল্লেখ আছে। পায়ুকামকে ৩৭৭ ধারায় প্রকৃতি-বিরুদ্ধ যৌন-আচরণ (Carnal intercourse against the order of nature) হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। পায়ুকাম এবং পায়ুধর্ষণের মধ্যে পার্থক্যের সীমারেখা টানা হয়নি। আইনে বলা হয়েছে –“In this crime question of consent has no value. Both the active and passive agents will be punished even when the act has been done with the consent of the passive agent”U. B. Mukherjee). এখানেই শেষ নয়, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারার আরও একটি বিষয় হল ‘মুখমৈথুন’ (Oral Sex), এটি আইনত দণ্ডনীয়। এক্ষেত্রে সমকাম ও বিষমকাম হিসাবে কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ আইনে দেওয়া হয়নি। অথচ ভাবুন তো, বর্তমান যুগে মানুষের যৌনজীবনে মুখমৈথুন করে না এমন ‘কাপল’ খুঁজে পাওয়া অতি দুর্লভ ব্যাপার। বর্তমান কেন বলছি, প্রাচীন যুগে খাজুরাহো মন্দিরে লক্ষ করুন, সেখানে মুখমৈথুনের মুর্তি দেখা মিলবে। সঙ্গী পুরুষই হোক বা নারীই হোক, শিশ্ন বা লিঙ্গ যদি তাঁর মুখে স্থাপন করা হয়, তবে তা পায়ুকামের সমান। অপরাধ বলে গণ্য করা হয় ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুসারে। এই বিশেষ যৌনক্রিয়াকে ফেলাসিয়ো (Fellatio) বলে। আইনে ফেলাসিয়ো অপরাধ হলেও যোনিতে মুখস্থাপন বিষয়ে অবশ্য আইন একেবারে চুপ। বাৎসায়নের ‘কামশাস্ত্রম্’-এও মুখমৈথুনের উল্লেখ আছে। তাহলে কোন্ যুক্তিতে মুখমৈথুন এবং মুখমেহন দণ্ডনীয় অপরাধ হবে বোধগম্য হয় না। তবে অনিচ্ছুককে দিয়ে মুখমৈথুন করানোটা নিশ্চয় অপরাধ হওয়া উচিত।
১১ ডিসেম্বর, ২০১৩ সালের এক রায়ে সুপ্রিম কোর্ট সমকামিতাকে অপরাধ বলেই গণ্য করতে বলে। দেশের সর্বোচ্চ আদালত জানান, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা অনুযায়ী সমকামিতা দণ্ডনীয় অপরাধ। যতক্ষণ না সংসদ আইন করে এই ধারা লোপ করছে ততক্ষণ সমকামিতা আইনত অপরাধই থাকছে। এর আগে ২০০৯ সালে দিল্লি হাইকোর্ট ৩৭৭ ধারার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছিল। ওই রায়ে বলা হয়েছিল, ভারতীয় দণ্ডবিধির এই ধারাটি বৈষম্যমূলক এবং মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী। দিল্লি হাইকোর্টের এই রায়ের সুবাদেই সমকামী এবং রূপান্তরকামীরা তাঁদের অধিকার অর্জনের পথে এগিয়েছিলেন বলে দাবি করতেন। সুপ্রিম কোর্টের এই বক্তব্য সেই এলজিবিটি আন্দোলনকারীদের পক্ষে বড়ো ধাক্কা। শীর্ষ আদালতের বেঞ্চের বক্তব্য– “৩৭৭ ধারা বাতিল নয়। ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী সমকামিতা দণ্ডনীয় অপরাধ, সাজা হতে পারে যাবজ্জীবন পর্যন্ত।”
কী আছে ৩৭৭ নম্বর ধারায়? একটু দেখে নেওয়া যাক– “Unnatural offences– whoever voluntarily has carnal intercourse against the order of nature with any man, women or animal, shall be punished with imprisonment for life, or with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine. Explanation– Penetration is sufficient to constitute the carnal intercourse necessary to the offence described in this section.”
প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশেও দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা অনুযায়ী, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোনো পুরুষ, নারী বা জন্তুর সঙ্গে, প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে যৌন সহবাস করে সেই ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে বা যে-কোনো বর্ণনার কারাদণ্ডে— যার মেয়াদ দশ বছর পর্যন্ত হতে পারে— দণ্ডিত হবে এবং তদুপরি অর্থদণ্ডেও দণ্ডনীয় হবে। এই ধারায় অস্বাভাবিক অপরাধের শাস্তির বিধান করা হয়েছে এবং তা অবশ্য প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধভাবে হতে হবে। যদিও প্রাকৃতিক নিয়ম বিরুদ্ধ যৌন সহবাসের সর্বজনীন স্বীকৃত সংজ্ঞা এখনও নির্ণীত হয়নি।
বর্তমানে বহু সমকামী সেক্সচেঞ্জ করে বিয়ে করে ঘর-সংসার করছে। আসুন, দেখে নিই দেশে দেশে সমকামী ও সমকামীদের আইনি অবস্থান :
নেদারল্যান্ডস : ২০০১ সালে বিশ্বের প্রথম দেশ হিসাবে নেদারল্যান্ডস্ সমকামী বিয়ে বৈধ ঘোষণা করে।
ইংল্যান্ড : ২০১৩ সালের জুলাই মাসে সমকামী বিয়ে বৈধ করে আইন পাস হয়।
ফ্রান্স : ২০১৩ সালের মে মাসে সমকামী বিয়ের বৈধতা দেওয়া হয়।
লুক্সেমবার্গ : ২০১৫ সালের জানুয়ারি মাসে সমকামী বিয়েকে বৈধতা দেওয়া হয়।
আয়ারল্যান্ড : বিশ্বের প্রথম দেশ হিসাবে আয়ারল্যান্ড ২০১৫ সালের মে মাসে গণভোটের মাধ্যমে সমকামী বিয়েকে বৈধ করা হয়।
ইউরোপের অন্যান্য দেশ : ২০০৩ সালে বেলজিয়াম, ২০০৫ সালে স্পেন, ২০০৯ সালে নরওয়ে ও সুইডেন, ২০১০ সালে পোর্তুগাল ও আইসল্যান্ড, ২০১২ সালে ডেনমার্ক, ২০১৪ সালে ফিনল্যান্ড এবং ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে গ্রিসে সমকামী বিয়ের বৈধতা দেওয়া হয়।
দক্ষিণ আফ্রিকা : আফ্রিকা মহাদেশের একটি দেশ দক্ষিণ আফ্রিকায় ২০০৬ সালে থেকে সমকামী বিয়ে বৈধ।
আর্জেন্টিনা : লাতিন আমেরিকার প্রথম দেশ হিসাবে ২০১০ সাল থেকে সমকামী বিয়ে বৈধ।
ব্রাজিল : ২০১০ সাল থেকে সমকামী বিয়ে বৈধ।
যুক্তরাষ্ট্র : ২০১৫ সালের জুন মাসে গোটা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে সমকামী বিয়ে বৈধ ঘোষণা করে দেশটির সুপ্রিম কোর্ট।
নিউজিল্যান্ড : এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের একমাত্র দেশ নিউজিল্যান্ডে ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে সমকামী বিয়ে বৈধ করা হয়।
এছাড়া মেক্সিকো (২০০৯), উরুগুয়ে (২০১৩), স্কটল্যান্ড (২০১৪), গ্রিনল্যান্ড (২০১৫), কলম্বিয়া (২০১৬), অস্ট্রেলিয়া (২০১৭), মালটা (২০১৭), অস্ট্রিয়া (২০১৭), এবং জার্মানে (২০১৭) সমকামী বিয়ে বৈধতা পায়।
পরিশেষে বলব– সাধারণ মানুষের কাছে এরা প্রান্তিক, এরা হিজড়া অথবা সমকামী। তাই এদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাজনিত উৎকণ্ঠা ও উদবেগ খুব সাধারণভাবেই লক্ষ করা যায়। দ্বৈতসত্ত্বার টানাপোড়েনে খোজারা জর্জরিত। এঁদের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতা যেমন প্রকট, তেমনি হীনমন্যতা কুরে কুরে খায়। বেশিরভাগ খোজাই যেহেতু পরিস্থিতির চাপে লিঙ্গ কর্তন করে হিজড়া সম্প্রদায়ের বাসিন্দা হয়, তাই তাঁরা এ জীবন সহজভাবে মেনে নিতে পারে না। উৎকণ্ঠা চেপে ধরে ক্রমাগত, প্রতি মুহূর্ত। হিজড়ারা মূলত সমকামী –একথা বলার অপেক্ষা রাখে না, সুস্থ যৌনজীবনে এঁরা অক্ষম বলেই সমকামী মানসিকতার শিকার। সেই কারণেই তথাকথিত পরিশীলিত সমাজের মানুষেরা এদের নারীর বিকল্প হিসাবে ভাবে। এই উপেক্ষিত হিজড়ারা মূলস্রোতের মানুষদের কাছ থেকে স্নেহ-ভালোবাসা-সম্মান পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে। বিনিময়ে মূলস্রোতের মানুষেরা এদেরকে কৌতুকের বস্তু মনে করে, হিজড়া আর জোকার যেন সমার্থক। তার উপর এঁদের সম্বন্ধে বিপুল অজ্ঞতার কারণে দূরত্ব বেড়েই চলেছে। আর এই অজ্ঞতার ফলেই এদের নিয়ে চটুল রসিকতা। ছেলেছোকারা এঁদের দেখলেই “এই আমারটা একটু চুষে দিবি?” বলে লেগপুলিং করে। এদেরকে মানবিক আন্তরিকতা ও সহানুভূতির সঙ্গে দেখার কথা কেউ ভাবতে পারে না। নানা রকমের কটুক্তি, কু-ইঙ্গিতের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষ এদের উত্যক্ত করে, উত্তেজিত করে। সমাজের অনেকেই হিজড়াদের ‘অশুভ শক্তি ভাবে। আবার কেউ কেউ অশুভ বা অপয়া তো নয়ই, উলটে শুভ বা পয়া ভাবে। কারোর কারোর মধ্যে হিজড়াদের শ্রদ্ধা করার রেওয়াজও আছে।
সারা পৃথিবীতে (বিশেষ করে ভারতে) উভলিঙ্গ মানবদের প্রাপ্য অধিকার ও মানুষ হিসাবে পুনর্বাসনের জন্য বিশেষ আইনের খুব প্রয়োজন, সনাতন লৈঙ্গিক বলয় ভাঙারও প্রয়োজন। ঘৃণা নয়, অবজ্ঞা নয়– শুধু মানুষ পাক মানুষের সম্মান। সার্বিক উন্নতির জোয়ারে প্লাবিত হলেও আমরা এখনও পুরোপুরি বিজ্ঞানমনষ্ক হয়ে উঠতে পারিনি। আমাদের দেশে কিছুদিন আগেও সমকামিতা নিষিদ্ধ বিধায় হিজড়াদের যৌনজীবন ছিল অপ্রতিষ্ঠিত। ভাবলে তখন অবাক লাগে যখন দেখি মানুষের যৌনজীবনে রাষ্ট্র নাক গলায়। একটা রাষ্ট্র বলে দেবে একজন মানুষ কীভাবে, কখন যৌনমিলন করবে? একটা রাষ্ট্র বলে দেবে একজন মানুষ যৌনসঙ্গী বা সঙ্গিনীর সঙ্গে কীরকম যৌনাচরণ করবে? রাষ্ট্র বলে দেবে কে মুখমৈথুন করবে, কে পায়ুমৈথুন, কে উরুমৈথুন করবে, কে স্তমৈথুন করবে, কে জননাঙ্গমৈথুন করবে? এসব কি রাষ্ট্রের নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে নাকি মানুষ? রাষ্ট্র সেখানেই নাক গলাতে পারে যেখানে যৌনমিলনের নামে অত্যাচার চলে, জোরজবরদস্তি চলে। যদি যৌনসঙ্গীর কেউ একজন তেমন অভিযোগ করে যে তাঁকে দিয়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো বিশেষ যৌনাচরণে বাধ্য করাচ্ছে। তা সে সমকামীদের ক্ষেত্রেই হোক, কিংবা বিপরীতকামী। এই যে সমকামীরা লোক দেখা নেই জন দেখা নেই যাকে-তাকে সমকাম করার জন্য বিরক্ত করে মারে– এটা অবশ্যই দণ্ডনীয় অপরাধ হওয়া উচিত, সাধারণ নারী-পুরুষের যৌনতা সংক্রান্ত দণ্ডবিধিতে যেমন শাস্তির বিধান আছে। তাই বলে সমকামকে স্বীকৃতি দিলে পায়ুমৈথুনকে স্বীকৃতি দিতে হবে, সেই কারণে সমকাম নিষিদ্ধ –এ যুক্তি কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। সমকাম এবং সমকামীদের স্বীকৃতি দিলে কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে? স্বীকৃতি দিলে পৃথিবীর সকলে লাইন দিয়ে সমকামী হয়ে যাবে? যদি তর্কের খাতিরে ধরেই নিই পৃথিবীর সকলে সমকামী হয়ে যাবে, তাতে কার কী এসে যাবে? সূর্য কি পশ্চিমদিক থেকে উঠতে শুরু করে দেবে? সন্তানের জন্ম? বিপরীতকামীদের মধ্যে কত হাজার হাজার দম্পতি সন্তানের জন্ম দিতে অপারগ, সে কারণে কি পৃথিবী রসাতলে চলে গেছে? খুবই অবাক লাগে মানুষের ব্যক্তিগত গণ্ডীর কামনা-বাসনা যখন সমাজ ও রাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার জালে আটকে থাকে এবং তাঁদের স্বীকৃতির অপেক্ষায় ধুকে ধুকে মরে। চিলেকোঠার খাঁচায় ডানায় গুলিবিদ্ধ অবস্থায় অসুস্থ হয়ে যেই পাখিটি এখনও কাতরাচ্ছে সেও স্বপ্ন বুনে আকাশে পুনরায় ডানা মেলার। তারও পূর্ণ অধিকার আছে ফিরে যাওয়ার তার জগতে। লাঞ্ছনা, বঞ্চনার জগত থেকে নানা প্রতিবন্ধকতার মাঝেও অস্তিত্বের বৈধতার সংগ্রাম করে চলছে হিজড়ারা। হাজার হাজার শিখণ্ডী চোখের দ্যুতির মাঝে স্বপ্ন লালন করে চলছে সম্মান ও সমৃদ্ধির জীবনের, একটি ঘর-সংসারের।
আজ অনিবার্য হয়ে উঠেছে হিজড়াদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার মানবিক দাবিটাও। রূপান্তরী মানবী বন্দ্যোপাধ্যায় চাকরিস্থলে তৃতীয় লিঙ্গ হিসাবে আইডেন্টটি করেছেন। ৩৭৭ নম্বর ধারার কবলে পড়ে আমার যে সমস্ত ভাই-বোন-বন্ধুরা যৌন-অবদমিত হয়ে বন্দিদশায় দিন কাটাচ্ছেন আমি বিপরীতকামী হয়েও তাঁদের পাশে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করি। তাঁদের মানসিক যন্ত্রণা আমি উপলব্ধি করি। আমি তাঁদের যৌনভাবনাকে সম্মান করি, সমর্থনও করি। কারণ আমি মনে করি ওদের যৌনচেতনা প্রাকৃতিকই। যৌন-প্যাশানে আমাদের মতো নিশ্চয় নয়, ওদের মতো তো বটেই! ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সমকামীদের দাবি অন্যায্য বলেছেন একদা। বস্তুত সুপ্রিম কোর্টের এই রায় মানুষের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপের সমতুল। মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত পরিসরে এ ভাবে ঢুকে পড়ার অধিকার বিচারব্যবস্থারও থাকতে পারে নাকি! প্রান্তবয়স্ক দুজন মানুষ তাঁদের যৌনজীবনে কী কী স্বাধীনতা নেবেন সে ব্যাপারে কেন মন্তব্য করবে আদালত? তাঁদের মতো করে যৌনতা করলে কেন সমকামীদের শাস্তি দেওয়া হবে? একজন পুরুষ নারীকে আদর না-করে কোনো পুরুষকে আদর করলে কিংবা একজন নারী যদি পুরুষকে আদর না করে কোনো নারীকে আদর করে, তবে তাঁদের জেল দিতে হবে? এটা কেমনতর অপরাধ! এর বিরুদ্ধে শুধু সমকামীরা নয়, প্রতিবাদ করা উচিত সমাজের সর্বস্তরের মানুষদের। আইনি বিশেষজ্ঞেরা স্পষ্টই বলছেন, সংবিধানের ১৪, ১৫ ও ২১ ধারা ব্যক্তি মানুষের যে সমানাধিকার ও স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়, সুপ্রিম কোর্টের এই রায় তার পরিপন্থী। এটা তো একটা ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের বিষয়। সেই পছন্দ তো অন্য কেউ করে দিতে পারে না। তবে হ্যাঁ, শুধু সৃষ্টি অর্থাৎ সন্তানধারণই যদি হয় ভালোবাসার সংজ্ঞা হয়, তা হলে তো অনেক কিছুই অস্বাভাবিক। শীর্ষ আদালত ভারতীয় দণ্ডবিধির যে ধারাকে সাংবিধানিক বলে বহাল রেখেছে, তা কেবল মাত্র পুরুষ বা নারীর সমকামিতার কথা বলে না। সেখানে বিষমকামিতার কথাও বলা আছে। সে ক্ষেত্রে ওরাল সেক্স ও অ্যানাল সেক্সও কিন্তু অপরাধযোগ্য। কারণ তাতে সৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই ভালোবাসা বা প্রেমের একমাত্রিক অভিমুখের বাইরে কিন্তু দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা ভাবছেন না।
১৬৩ বছর আগে ব্রিটিশ ভারত একে অপরাধ বলে গণ্য করেছিল। তার আগে পর্যন্ত কিন্তু সমকামিতা নিয়ে ভারতীয় সমাজে সেভাবে কোনো হেলদোল ছিল না। প্রাচীন বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ভারত যেখানে চিন্তার দিক থেকে এতটা অগ্রসর ছিল, তা হলে একবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে কেন সুপ্রিম কোর্টের এহেন রায়? কেন পুরুষের সঙ্গে পুরুষ বা মহিলার সঙ্গে মহিলার সম্পর্ককে এখনও ‘প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধাচারণ ভাবা হচ্ছে? সুপ্রিম কোর্টের রায় বলছে— তাঁরা ভরসা করেছে ১৮৬০ সালের মেকলের ব্যাখ্যাকেই। তিনি বলেছিলেন, ‘যৌনতা সৃষ্টির জন্য, কোনো বিনোদনের জন্য নয়। এ ধরনের সম্পর্ক থেকে কোনও সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। কাজেই এই সম্পর্ক প্রাকৃতিক নয়। শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তার মানে সৃষ্টি হয়ে গেলে যৌনমিলন বন্ধ দেওয়া উচিত, তাই নয় কি? কন্ডোম বা অন্যান্য জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে যৌনমিলন করার উদ্দেশ্য তো বিনোদনই। পাঠক ভালো করে লক্ষ করুন এই লাইনটি– “যৌনতা সৃষ্টির জন্য, কোনো বিনোদনের জন্য নয়। এ ধরনের সম্পর্ক থেকে কোনো সৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। কাজেই এই সম্পর্ক প্রাকৃতিক নয়।” যৌনতা সৃষ্টির জন্য? কবে থেকে? বাজারে, থুড়ি আমাদের মনুষ্যসমাজে এমন একটা কথা চালু আছে বইকি। আমিও শুনেছি। হিপোক্রাসি, জাস্ট হিপোক্রাসি। ভণ্ডামি। দেখো, আমরা মানবজাতি কী মহান উদ্দেশ্যই-না যৌনক্রীড়া করি, এটা বোঝাতেই বোধহয় এই গপ্পো সমাজে ছড়িয়ে আছে। যখন বা যেদিন যে আদি মানব-মানবীটি প্রথম যৌনক্রীড়া করেছিল সেটাই তো ছিল স্রেফ যৌনতাড়না। ওরা সৃষ্টির জন্য যৌনক্রীড়া করেছে বলে কোথাও উল্লেখ পাইনি। শিবপুরাণে শিব-পার্বতীর যে দীর্ঘ সময় একটানা যৌনক্রীড়ার বর্ণনা পাওয়া যায় তাতে কোনো সৃষ্টির কাহিনি বর্ণিত নেই। বরং সৃষ্টি স্তব্ধ হয়ে যাবে এই আতঙ্কে স্বয়ং বিষ্ণু শিব-পার্বতীর বেডরুমে শুকপাখিকে পাঠিয়ে দেয় তাঁদের যৌনক্রীড়া ঘেঁটে দেওয়ার জন্য।
বিপরীতকামীরা যদি বলেন তারা শুধুই সৃষ্টির জন্যই যৌনক্রীড়া করেন, তা করুন না। সমকামীদের যৌনতায় যদি কিছু সৃষ্টি না হয় তাতে বিপরীতকামীদের অসুবিধাটা কোথায়? ওরা তো কারোর পাকা ধানে মই দিচ্ছে না! আপনি বা আপনারা বা আদালত বা রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিন বা না-দিন তাতে তো ওদের সৃষ্টিহীন যৌনতা বন্ধ থাকবে না। পৃথিবীও রসাতলে যাবে না– স্বীকৃতি দিলেও না, স্বীকৃতি না দিলেও না। আপনার পছন্দ নয় বলে তো বিকল্প যৌনতা মিথ্যা হয়ে যাবে না। আপনার পছন্দ নয় বলে আপনি কোনো একজনের জীবনও বিপন্ন করে তুলতে পারেন না। সেই অধিকার আপনার। নেই। মনে রাখবেন, বিপরীতকামীদেরই সৃষ্টির উদ্দেশ্যে যৌনতার ফলে যে হাজার হাজার সন্তান পিতৃমাতৃপরিচয়হীন হয়ে অনাথ আশ্রমগুলিতে অনাদরে অসহায় হয়ে আছে, প্রয়োজন হলে ওই সমকামী দম্পতি সেইসব সন্তান দত্তক নিয়ে বাবা-মা হওয়ার অহংকারে অহংকারী হবেন। আমিও চাই সমকামী দম্পতিরা সন্তান দত্তক নিয়ে পিতা-মাতার সাধ মেটাক।
সৃষ্টির জন্য যৌনক্রীড়া, বিনোদনের জন্য নয় –এই বক্তব্যের সমর্থনে কোনো দৃষ্টান্তই আমি উপস্থাপন করতে পারছি না। মানুষ মূলত উদ্ধৃঙ্খল যৌনাচারকে শৃঙ্খলিত-বৈধতা দেওয়ার জন্যই বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি করেছিল। শুধু বৈধ যৌনতাই নয়, সন্তানের পিতৃ-পরিচয় নিশ্চিত করতেও বিবাহের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। মানুষ শুধুমাত্র সৃষ্টির জন্যই যৌনতা করে না, করে না-বলেই মানুষের জন্য যৌনক্রীড়ার সময় ৭ X ২৪ x ৩৬৫ দিনই। সৃষ্টির জন্য যৌনক্রীড়া করে না, তাই অনেক অবিবেচক পাষণ্ড মানুষ ঋতুচক্র চলাকালীনও মিলিত হন। সৃষ্টির জন্য যৌনক্রীড়া করে না-বলেই গর্ভবতী হয়ে পড়লেও যৌনক্রীড়া বন্ধ করে না। সৃষ্টির জন্য যৌনক্রীড়া করে না-বলেই অনেকে বিবাহ বহির্ভূত যৌনতা করে থাকে। সৃষ্টির জন্য যৌনক্রীড়া করে না-বলেই অনেক নারী বা পুরুষ একাধিক পুরুষ বা নারীর সঙ্গলাভের প্রত্যাশা করে। মানুষ সৃষ্টির জন্য যৌনক্রীড়া করে না-বলেই সারা পৃথিবী জুড়ে গণিকাপল্লি বা। গণিকাবৃত্তির এত রমরমা। গণিকাপল্লিতে কেউ নিশ্চয় সৃষ্টি করতে যায় না! প্রতিদিন সকালে খবরের কাগজের পাতায় যৌন কেলেঙ্কারীর খবরগুলি আমরা পাই সেগুলি নিশ্চয় সৃষ্টির জন্য বলবেন না। এত যে ধর্ষণকাণ্ড (জোরপূর্বক যৌনক্রীড়া) ঘটে যায় গোটা পৃথিবী জুড়ে প্রতিদিন কোথাও-না-কোথাও, তা কি সৃষ্টির জন্য? তবে প্রাচীনকালে নিয়োগ প্রথার মাধ্যমে শুধুমাত্র সন্তান সষ্টির জন্যই যৌনমিলন করতে হত। এটি ছিল বিশেষ শর্তসাপেক্ষ যৌনমিলন। পাণ্ডবের পাঁচজন, কৌরবদের ১০১ জন, কর্ণ, রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন প্রমুখরা তো নিয়োগ প্রথারই ফসল। এই ব্যতিক্রমী যৌনমিলনগুলি অবশ্যই শুধুমাত্র সৃষ্টির জন্য ছিল। এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।
একটা সুস্থ মানুষ তার সমগ্র জীবনে (কমবেশি) ১০,০০০ থেকে ১১,০০০ যৌনদিবস (নিশি?) পান। তার মধ্যে মাত্র ৩০ দিন থেকে ৯০ দিন সৃষ্টির জন্য ব্যয় করেন। বাকি যৌনক্রীড়ার দীর্ঘ দিনগুলি শুধুই যৌনানন্দ বা যৌনবিনোদন বা যৌনসুখের জন্য অতিবাহিত করে থাকে। তাই পাত্র বা পাত্রী যৌনক্রীড়ায় অক্ষম হলে কোনো ক্ষমা নেই। সোজা ডিভোর্সের মামলা। সন্তান উৎপাদনে অক্ষম হলে ডিভোর্স হয় কি না আমার জানা নেই, তবে পাত্র বা পাত্রীর যে কেউ একজন যৌনক্রীড়ায় অক্ষম হলে এক লহমায় সম্পর্ক শেষ। যে যুগে মানুষের যৌনক্রীড়া মানেই অনিবার্য সন্তানের জন্ম হত, সে যুগে মানুষ নিশ্চয় খুব অসহায় ছিল। সেই অসহায়ত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হল। মানুষের সেই অসহায়তা এখন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত। সারা পৃথিবী জুড়ে রক্তপাতহীন বিপ্লব ঘটে গেল। বাজারে এখন হাজারটা জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা সুলভে পাওয়া যায়, যার যার সুবিধামতো। এইসব প্রোডাক্টের বিক্রিবাটাও ব্যাপক। এমন কি স্রেফ যৌনসুখ করতে গিয়ে সন্তান যদি এসেও যায় সমূলে বিনাশ করার তারও ব্যবস্থা পর্যাপ্ত মজুত আছে। সন্তানহীন (পড়ুন সৃষ্টিহীন) যৌনসুখ পেতে মানুষ কি-না করছেন! এরপরেও কেউ যদি বলে সৃষ্টির জন্যই যৌনতা, তাহলে বলব ওসব হিপোক্রাসি ঝেড়ে ফেলে আসুন প্রান্তিক হয়ে যাওয়া মানুষের পাশে দাঁড়াই। মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে সামিল হই। ভারত পথ-প্রদর্শক হতে পারত, তার বদলে ভারত এখন ক্রমশ পিছন দিকে এগোতে চাইছে। একে চূড়ান্ত পশ্চাদগামী মানসিকতা’ ও ‘লজ্জা’ ছাড়া অন্য কোনও ভাষায় ব্যাখ্যা করা যায় না। ভুললে চলবে না— চোখ বন্ধ রাখলে প্রলয় থেমে থাকে না।
প্রায় ১৫০ বছর ধরে আমাদের চোখ বন্ধই ছিল। অবশেষে ২০১৮ সালের ৬ সেপ্টেম্বর চোখ খুলল সুপ্রিমকোর্টের এক ঐতিহাসিক রায়ে। সুপ্রিমকোর্ট স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন –“Gay sex is not a crime. Gay sex is legal in India now.”। সুপ্রিমকোর্টের প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্রের মন্তব্য– “পুরোনো ধ্যানধারণাকে বিদায় দিয়ে সমস্ত নাগরিকদের সমান অধিকার আমাদের দিতে হবে।” বিচারপতি দীপক মিশ্রের সঙ্গে সহমত পোষণ করে একই বক্তব্য রেখেছেন অন্য চার বিচারপতিও। একই সঙ্গে তাঁরা জানিয়েছেন– “ব্যক্তিগত পছন্দ স্বাধীনতার অন্যতম শর্ত। ভারতীয় সংবিধানে এলজিবিটি গোষ্ঠীর সদস্যরা বাকিদের মতো একই অধিকার পাওয়ার যোগ্য।”
এলজিবিটি সমাজে এখন উৎসবের মেজাজ। মুক্তির আনন্দ। কিন্তু এঁদের এই আনন্দ সোজা-সরল পথে আসেনি। আসুন, সেই অসম লড়াইয়ের কাহিনি জেনে নিই। ১৯৯৮ সালে ম্যাসাচুসেটসের ক্লার্কস ইউনিভার্সিটি থেকে ডাবল মেজর করে ভারতে ফিরে আসার পর আয়েশা কাপুর যোগ দিয়েছিলেন ই-কমার্স খাতে, যা তখন এ দেশে সবে মাথা তুলছে। খুব শীঘ্রই বিজনেস হেডের পদে পৌঁছোতেও কোনো অসুবিধা হয়নি তাঁর। কিন্তু দশ বছরের মধ্যেই ছবিটা পাল্টে গেল –যখন তাঁর সেক্সয়াল ওরিয়েন্টেশানের কথা জানাজানি হয়ে গেল। এর ফলে তাঁকে চাকরি ছাড়তে হয়। আয়েশার সঙ্গী ছিলেন একজন মহিলা পরে স্বাধীনভাবে ব্যাবসা করে তিনি ভারতের কর্পোরেট জগতে দারুণ সফল ঠিকই, কিন্তু নিজের সঙ্গীকে নিয়ে সামাজিক ও পারিবারিক কোনো অনুষ্ঠানে যেতে তাঁকে সমস্যায় পড়তে হয়।
অথচ ২০১৩ সালে ভারতেই এই সর্বোচ্চ আদালতই দিল্লি উচ্চ আদালতের একটি আদেশ খারিজ করে দিয়ে বলেছিল– ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের ৩৭৭ ধারা (যে ধারায় সমকামিতাকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য করা হয়েছে) বাতিল করার কোনো অধিকার আদালতের নেই। কারণ সেই দায়িত্ব পার্লামেন্টের। সেই রায়ের বিরুদ্ধেই সর্বোচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হন বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আসা দেশের পাঁচজন সেলিব্রেটি, যাঁদের অন্যতম ছিলেন আয়েশা কাপুর। তাঁদের পিটিশনে তাঁরা সুপ্রিমকোর্টেরই নিজেদের রুলিং পুনর্বিবেচনার আর্জি জানান। সেই পিটিশনে সুপ্রিম কোর্ট ৩৬০ ঘুরে গিয়ে রায় দিলেন পূর্বের মত বদলে। এই পাঁচজন তারকার আইনি লড়াইয়ে সুবাদেই যে আজ ভারতের লক্ষ লক্ষ সমকামী মানুষ তাঁদের মতো জীবনযাপন করতে পারবেন। যাপন করতে পারবেন মতো করে যৌনজীবন। কিন্তু কারা সেই পাঁচজন? তাঁদের কথা খোদিত করে না রাখলে ইতিহাস ক্ষমা করবে না।
নভতেজ সিং জোহর : ৫৯ বছর বয়সি নভতেজ সিং জোহর ভারতের একজন প্রখ্যাত ধ্রুপদী নৃত্যশিল্পী। ভারতনাট্যম নৃত্যে অসাধারণ অবদানের জন্য সঙ্গীত নাটক একাডেমি পুরস্কারেও ভূষিত তিনি। গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে যে সঙ্গীদের সঙ্গে রয়েছেন তিনি, তাঁদের সঙ্গে মিলেই সুপ্রিমকোর্টে পিটিশনটি দাখিল করেছিলেন তিনি। তাঁর যুক্তি ছিল, ভারতের সংবিধান যে জীবনের অধিকার ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অঙ্গীকার করে, ৩৭৭ ধারা সেই অধিকারের পরিপন্থী।
সুনীল মেহরা : সাংবাদিক সুনীল মেহরার বয়স ৬৩। তিনি একসময় ম্যাক্সিম ম্যাগাজিনের ভারতীয় সংস্করণের সম্পাদক ছিলেন। সুনীলের সঙ্গে নভতেজের সাক্ষাৎ হয়েছিল ১৯৯৪ সালে। প্রথম দেখা হওয়ার ছয় মাস পর থেকেই তাঁরা একসঙ্গে থাকতে শুরু করেন। সেই জুটি আজ প্রায় সাতাশ বছর পরেও ভাঙেনি।
রিতু ডালমিয়া : ৪৫ বর্ষীয় রিতু ডালমিয়া ভারতের নামী সেলিব্রেটি শেফদের অন্যতম। তাঁর ‘ডি’ রেস্তোরাঁ চেইন ভারতে সেরা ইটালিয়ান খাবারের অন্যতম ঠিকানা বলে মনে করা হয়। রিতুর জন্ম কলকাতার এক রক্ষণশীল মারোয়াড়ি পরিবারে। তিনি নিজেকে পরিচয় দেন লেসবিয়ান হিসাবে। তিনি যে লেসবিয়ান সে কথা নিজের পরিবারের কাছে ঘোষণা করেছিলেন একদিন ডিনারের টেবিলে বসে। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাঁর বাবা-মাও বিষয়টা সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি।
আমন নাথ : ৬১ বর্ষীয় আমন নাথও এই পিটিশনে যুক্ত ছিলেন। আমন নাথ ভারতের নিমরানা হোটেল চেইনসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও কর্ণধার। তবে শুধু হোটেলিয়ার হিসাবেই নয়, শিল্পরসিক ও ইতিহাসবিদ হিসাবেও তাঁর খ্যাতি দুনিয়া জোড়া। শিল্পকলা, ইতিহাস, স্থাপত্য ও ফোটোগ্রাফির মতো বহু বিষয়ে তিনি অজস্র বই লিখেছেন।
আয়েশা কাপুর : আয়েশা ছিলেন সুপ্রিমকোর্টে দাখিল করা পিটিশনের পঞ্চম মুখ। ই-কমার্সের জগৎ ছেড়ে দেওয়ার পর আয়েশা এখন যুক্ত ফুড অ্যান্ড বিভারেজ ইন্ডাস্ট্রিজের সঙ্গে। আর সেখানেও তিনি ভীষণ সফল। এই যে ভারতের এলজিবিটিরা ৩৭৭ ধারাকে বিলুপ্ত করে নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা অনুযায়ী জীবনযাপনের অধিকার পেলেন, তার জন্য তাঁরা অবশ্যই এই পাঁচজনের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন।
সুপ্রিমকোর্টের ঐতিহাসিক রায়টা সত্যিই অনেকটা এগিয়ে দিল এলজিবিটিদের। বাকি রইল সামাজিক টানাপোড়েন। সেটা আমাদেরই মেরামত করতে হবে। কিন্তু আইন কবেই-বা সমাজকে বদলাতে পেরেছে! আমরা কি পারব ওদের দেখে মুখ টিপে হাসি বন্ধ করতে? আমরা কি পারব ওদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা বন্ধ করতে? এফিমিনেট ছেলেটিকে দেখে বলব না তো ‘হাফ লেডিজ’? আমরা এলিজিবিটি মানুষদের যৌন স্বাধীনতায় কাঠি দিতে যাব না তো? এলজিবিটিদের আমরা জোর করে নারী ও পুরুষ বানাতে যাব না তো? তাঁদের মানুষের সম্মান ও মর্যাদা দেব তো?
আপাতত এলজিবিটিদের জন্য আইন তো পাশে রইলই। সেটাও কম বড়ো আত্মরক্ষার অস্ত্র নয়। তবে আইন তাঁদের পক্ষে থাকলেও বিপদ একেবারে মুক্ত হয়ে গেছে একথা বলা যায় না। ভারতীয় জনতা দলের সভাপতি (বিজেপি) রাজনাথ সিংহ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন –“We will state (at an all party meeting if it is called) that we support Section 377 because we supported.” রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ (আরএসএস) তাঁদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছে –“Homosexuality not a crime, but it’s not natural. Gay marriage and relationship are not compatible with nature and are not natural, so we do not support this kind of relationship. Traditionally, India’s society also does not recognize such relations.” অতএব চলার পথে ফুল ছড়ানো আছে মনে হলেও রক্তাক্ত হওয়ার মতো কাঁটা কিন্তু রয়েই গেছে।
———-
সাহায্যকারী তথ্যসূত্র : (১) ব্রহ্মভার্গবপুরাণ– কমল চক্রবর্তী।
(২) হলদে গোলাপ– স্বপ্নময় চক্রবর্তী।
(৩) Let us live : Social Exclusion of Hijra Community– Sibsankar Mali
(৪) অন্তহীন অন্তরীণ প্রোষিতভর্তৃকা– সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
(৫) ভারতের হিজড়ে সমাজ– অজয় মজুমদার ও নিলয় বসু।
(৬) The Truth About Me— A Hijra Life Story— A. Revathi, Penguin।
(৭) দেবদাসীতীর্থ– ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়।
(৮) অপরাধ জগতে ভাষা ও শব্দকোষ– ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক।
(৯) হিজড়ে কথা : রক্তমাংসের অসংগতি এবং– পিনি দাসগুহ, উৎস মানুস।
(১০) না-পুরুষ, না-মেয়ে মহাভারতের গোপন পর্ব– রমাপ্রসাদ ঘোষাল, প্রতিদিন।
(১১) নপুংসক— অনিরুদ্ধ ধর, সানন্দা।
(১২) পুরুষ যখন যৌনকর্মী– মজুমদার ও বসু।
অস্পৃশ্যনামা
“লোকানান্তু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহুরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশং শূদ্রঞ্চনিরবর্তয়ৎ।”
অর্থাৎ লোকবৃদ্ধির জন্য (স্রষ্টা) মুখ, বাহু, ঊরু ও পদ থেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সৃষ্টি করলেন।
এখানে পরিষ্কার। শূদ্রদের জন্মই হয়েছে পদ বা পা থেকে। নির্দেশ যাদের পা থেকে তাঁরা মাথায় উঠবে কীভাবে! তাই এঁদের স্থান তো পায়ের নিচেই হতে হবে! অতএব জন্মও পায়ের নিচে, কর্মও পায়ের নিচে।
গীতায় শ্রী ভগবানের উক্তি মতে বলা হয়েছে–”আমি গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে চার বর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) সৃষ্টি করেছি।” পুরুষ সুক্তের মন্ত্র ব্যাখ্যা করে নির্মল কুমার বসু যে মত ব্যক্ত করেন তা হল চারটি বিশেষ গুণসম্পন্ন এবং বিভিন্ন মাত্রার সং্যাগের ফলে চার বর্ণের মধ্যে গুণের তারতম্য দেখা যায়। প্রাচীন ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতের গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে সে জাতির কর্ম উল্লিখিত চার বর্ণের কর্মের সঙ্গে মিল না থাকলে সে জাতি মিশ্র গুণসম্পন্ন ধরে নেওয়া হত। তবে এক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয় তাদের বর্ণ ও সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণের ক্ষেত্রে। মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম প্রভৃতি স্মৃতিকার এ নিয়ে যে মতামত দেন তা প্রণিধানযোগ্য। মনু সংহিতায় স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। যে প্রত্যেক জাতির নির্দিষ্ট বৃত্তি ছিল এবং স্মৃতিকাররা বৃত্তির ভিত্তিতে সে জাতির বর্ণ ও সামাজিক মর্যাদা নির্ধারণ করে দিতেন। এর থেকে প্রমাণিত হয়, প্রাচীনকালে কিছু গুণকে উত্তম এবং কিছু গুণকে অধম বলে গণ্য করা হত। একইভাবে কিছু বৃত্তিকে শুদ্ধ এবং কিছু বৃত্তিকে অশুদ্ধ বলে বিবেচনা করা হত। এভাবে গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র–এ চার বর্ণের সৃষ্টি হয়।
ব্রাহ্মণদের প্রভূত্বকামী শাসনব্যবস্থা ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রধান অস্ত্রই হল চতুর্বর্ণ প্রথা। অর্থাৎ সমাজে চারটি বর্ণের উপস্থিতি— ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। এই প্রথার মাধ্যমে গোটা জনগোষ্ঠীকে এক অদ্ভুত বর্ণবৈষম্যের মধ্য দিয়ে বিভাজিত করে যে ‘ভাগ করো, শাসন করো’ নীতি কায়েম করা হয়েছে, সেখানে স্বঘোষিত বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণদের আধিপত্য প্রশ্নহীন করে রাখা হয়েছে। বর্ণ-মর্যাদার দিক থেকে এর পরই রাজদণ্ডধারী ক্ষত্রিয়ের অবস্থান। তার নিচে বৈশ্য এবং সর্বনিকৃষ্ট বর্ণ শূদ্র। মানব সমাজটাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে আগ্রাসনবাদী বৈদিক সমাজের সর্বগ্রাসী বর্ণ-বিভেদের ছায়ায়। গোটা মনুসংহিতার কোথাও কোনোভাবে মানুষ নামের কোনো স্বতন্ত্র সত্ত্বার বা মানব জাতির অস্তিত্ব প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায়, তা হচ্ছে— চারটি বর্ণভিত্তিক ব্রাহ্মণ জাতি, ক্ষত্রিয় জাতি, বৈশ্য জাতি ও শূদ্র জাতি। মনুসংহিতায় ‘ভগবান’ মনু যে চারটি বিষয়ে সবচেয়ে বেশি চিন্তিত ছিলেন, তা হল –ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, নারী এবং শূদ্র। এই চারটি ক্ষেত্রেই তিনি সবচেয়ে বেশি নির্দেশ দিয়েছেন। তবে চতুর্বর্ণের বাইরে আর-একটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব আছে, তা হল— অন্ত্যজ বা অস্পৃশ্য। অর্থাৎ অস্তিত্ব থাকলেও সমাজ যাকে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকার করে না।
বর্ণ ব্যবস্থায় একজন ব্যক্তি যে বর্ণে জন্মগ্রহণ করেন তার বাইরে অবস্থান গ্রহণের কোনো সুযোগ নেই। জন্মের দ্বারাই নির্ধারিত হয় যে, সে কোন্ বর্ণের অন্তর্ভুক্ত। অজানা সময় কাল থেকে একটি বংশধারা এই মর্যাদা ভোগ করে আসছে। অনন্তকাল পর্যন্ত বংশধারার মাধ্যমে এটা অব্যাহত থাকবে। ব্যক্তির মর্যাদা জন্ম দ্বারা নির্ধারিত। একজন ব্রাহ্মণ হিসাবে জন্মগ্রহণ করলে যে-কোনো অবস্থাতেই সে ব্রাহ্মণের জন্য নির্ধারিত মর্যাদা ও পুরস্কার ভোগ করবে। কোনো ব্যক্তি এক বর্ণে জন্মগ্রহণ করে অন্য বর্ণে বিয়ে করতে পারে না। কারণ বর্ণের বাইরে বিয়ে করলে তার বংশগত পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যায়। শুধু যে বংশগত পবিত্রতাই মূল কথা তাই নয়, এর সঙ্গে আরও বহু আচার ব্যবস্থা জড়িত, যার মাধ্যমে বর্ণ শুদ্ধতা রক্ষিত হয়। মূল বর্ণগুলির মধ্যেও আছে হাজারও উপবর্ণ। এই উপবর্ণগুলি আবার নিজেদের গোত্রগত বিশুদ্ধতা রক্ষার রীতিনীতি মেনে চলে। এই উপগোত্রগুলি আবার নিজেদের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য নানারূপ বিধিনিষেধ মেনে চলে যেমন সপিণ্ড, সগোত্র ইত্যাদি সংক্রান্ত আচার বিধি। এই নিয়ম কঠোরভাবে মানতে হয়, তা না হলে উঁচু জাতের পবিত্রতা বিনষ্ট হয়। বিশেষ করে ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণের মধ্যে এটা কঠোরভাবে মেনে চলা হয়। এজন্য পণ্ডিতরা বলে থাকেন, ভারতে বর্ণপ্রথার ইমারতটি গড়ে উঠেছে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের উপর। একজন ব্রাহ্মণ একজন নিচু জাতের লোকের সঙ্গে একত্রে বা হাতের রান্না খাবে না, ছোঁয়া খাবার খাবে না। তাঁর খাওয়া পাত্রে খাবে না, তাঁর স্পর্শ করা খাবার খাবে না। বর্ণ পঞ্চায়েত এবং আচরণরীতি ব্যাপারটার কেন্দ্রে রয়েছে ব্রাহ্মণ সমাজ এবং তাঁদের কৌলীন্য ও মর্যাদার ধারণার গুণগত উৎকর্ষের কারণে সমাজে মানুষ উচ্চতর মর্যাদা এবং পুরস্কারগুলি ভোগ করবে। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম, এটাই দস্তুর। একটি বিশেষ পুরস্কার বা সুবিধা বিশেষ গোষ্ঠীর জন্য নির্ধারিত থাকে। এর ফলে সমাজের নিম্ন শ্রেণিগুলির মধ্যে উচ্চতর অর্জন প্রেষণা কাজ করে না। সমাজ হয়ে পড়ে বদ্ধ জলাভূমি। এখানে সর্বস্তরের মানুষের মেধার সর্বোচ্চ ব্যবহার সম্ভব হয় না। মানুষের উচ্চ অর্জন প্রেরণা হচ্ছে সমাজ উন্নয়নের চাবিকাঠি। যেহেতু বর্ণ ব্যবস্থায় ব্যক্তির মর্যাদা এবং পুরস্কার শ্রম ও মেধার সাহায্যে অর্জন করা যায়, তাই সার্বিকভাবে সামাজিক সচলতার উপস্থিতি এখানে লক্ষ করা যায় না।
একজন প্রখ্যাত ব্রাহ্মণ কী বলছেন জেনে নেওয়া যাক। প্রখ্যাত সেই ব্রাহ্মণটির নাম গদাধর চট্টোপাধ্যায়। সবাই যাকে ‘রামকৃষ্ণ পরমহংস’ বলে জানে। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ লীলামৃত গ্রন্থের ২২৫ পৃষ্ঠায় শূদ্রের শয্যাত্যাগ বিষয়ে বলছেন– “পায়স গ্রহণোদ্যত, এমতকালে দেখেন লাটু ও গোপাল দাদা (বৰ্ণ বিচারে শূদ্র) শয্যাধারণ করিয়া আছেন। কহেন, ওদের বিছানা ছেড়ে দিতে বল। কেন করিবে! নরেন্দ্রের প্রশ্নে বলেন– ওরে! ভাত ভাত যে রে। আপনি তো বিধিনিষেধ পার, তথাপি এ আদেশ কেন? নরেন্দ্রনাথ নিবেদন করিলে ঠাকুর বলেন –ওরে ব্রাহ্মণ শরীর যে রে! তাই ব্রাহ্মণ-সংস্কার যাবার নয়। অগত্যা লাটু ও গোপাল দাদাকে শয্যা ছাড়িতে বলা হইল।”
এখানেই শেষ নয়, অন্ন-বিচারেও ‘ঠাকুর’ খড়হস্ত ছিলেন। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত থেকে –“যদিও বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত অনেক ভক্ত ছিলেন, তথাপি ঠাকুর সকলের আলয়ে অনুগ্রহণ করেন নাই। বলিতেন– লুচি-তরকারী খেতে পারা যায়, কিন্তু অন্ন নহে। কলিতে অনুগত পাপই মহাপাপ। কিন্তু দেখিয়াছি, পরমভক্ত বলরাম বসুর ভবনে জগন্নাথদেবের অন্নভোগ গ্রহণ করিতেন, বলিতেন– বৈষ্ণব বলে কুলপ্রথায় উহারা জগন্নাথ স্বামীকে অন্নভোগ দেয়, তাই উহা শুদ্ধান্ন। বলরাম মন্দিরে অনুগ্রহণ জানিয়া কোনো ভক্ত তাঁদের শালগ্রাম শিলার অন্নভোগ দিয়া তাঁহাকে সেবা করাইবার প্রস্তাব করিলে ঠাকুর কহেন– তোমার ত কুলপ্রথা নয়, কেবল আমাকে ভাত খাওয়াবার অভিলাষ, আবার তোমার দেখাদেখি অন্য ভক্তরাও এইরূপ করবে। তাহলে আমি সকল শূদ্র ভক্তবাড়িতে খেয়ে বেড়াই!” ঠাকুর রামকৃষ্ণ জাতবিচারে টনটনে ছিলেন। ব্রাহ্মণ বলে কথা! তিনি কোনোদিনই জাতঘৃণার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। যিনি সকলের হতে পারেন না, তিনি কী করে যে ‘যেই রাম সেই কৃষ্ণ হন, তা একমাত্র ভক্তরাই বলতে পারবেন।
বর্ণ ব্যবস্থায় বর্ণ দ্বারা নির্ধারিত হয় ব্যক্তির পেশা। এই বর্ণ ব্যবস্থায় ব্যক্তির মেধা অনুযায়ী পেশা নির্বাচনের কোনো অধিকার সেই ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর থাকে না। পেশা এখানে জন্মগত এবং বংশগতভাবে নির্ধারিত হয়। সমাজ থেকে ব্যক্তির উপর এক ধরনের প্রত্যাশার বাধ্যবাধকতা চাপিয়ে দেওয়া হয়, সে তাঁর গোত্র বা বর্ণের পেশাই গ্রহণ করবে। এই সেদিন পর্যন্ত ব্যক্তির পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হত না। এই বর্ণপ্রথায় ব্যক্তির মেধা, যোগ্যতা, শ্রমকুশলতা, আগ্রহ, সৃজনশীলতা কোনো গুরুত্ব পেত না। তাই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে যাঁর যা জন্মগত এবং বংশগত পেশা তাঁরা তাই করে যাচ্ছে, যে মানুষেরা মল বা বিষ্ঠা ফেলার কাজ করত সে তাইই করত (মেথর)। যে কাঠের কাজ করে সে তাই-ই করে যাচ্ছে (ছুতোর)। যে ক্ষৌরকর্মের কাজ করে তাঁর সন্তান-পরম্পরা তাই-ই করে যাচ্ছে (নাপিত)। যে মাছ ধরে বংশপরম্পরায় তাঁরা ওই পেশাই (জেলে) করে চলেছেন। যে মৃতদেহ দাহ করেন তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম তাই-ই করেন (ডোম)— পরিবর্তনের কোনো চিন্তাই করে না। তবে পরিবর্তন যে একেবারেই হচ্ছে না, তা কিন্তু নয়। এখন ব্রাহ্মণের ছেলেমেয়েকে সেলুনে চুল কাটতে যায়, তেমনি শূদ্ররাও তথাকথিত জাতির পেশা ত্যাগ করে অন্য পেশায় আসছেন।
বর্ণপ্রথা সমাজের অভ্যন্তরে নিদারুণ রকমের সামাজিক বিচ্ছিন্নতা তৈরি করেছে এবং করছে। একটা জাতি হাজার বিভাজনে বিভাজিত হয়ে আছে। যে মন্দিরে ব্রাহ্মণরা পুজো করবেন, সেই মন্দিরে শূদ্র তথা দলিতরা পুজো দিতে পারবে না। যে উৎস থেকে একজন ব্রাহ্মণ জল উত্তোলন করেন, সেখান থেকে একজন দলিত জল উত্তোলন করতে পারেন না। বাবা আম্বেদকরের এ অভিজ্ঞতা হয়েছিল, যা তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছে। কেরালাতে একজন ‘নায়ার’ একজন নাম্বুদারি ব্রাহ্মণের কাছে আসতে পারে, কিন্তু তাকে স্পর্শ করতে পারে না। একজন ‘তিয়া’ একজন ব্রাহ্মণ থেকে ৩৬ পদক্ষেপ দূরে থেকে কথা বলবে এবং একজন ‘পুলাইয়া’ একজন ব্রাহ্মণ থেকে ৯৬ পদক্ষেপ দূরে থেকে কথা বলবে। এর চেয়ে কম দূরত্বে আসতে পারবে না। পেশোয়া শাসন আমলে মহারাষ্ট্রে মাহার এবং মঙ সম্প্রদায়ভুক্ত নিম্নবর্গের মানুষদের শুধু সকাল ৯টার পর এবং বিকাল ৩টার আগে পুনা গেটে আসার অনুমতি ছিল, কারণ এর আগে মানুষের ছায়া অনেক দীর্ঘ থাকে এবং কোনো ব্রাহ্মণ যদি সে ছায়া অতিক্রম করে তাহলে তাঁর জাত নষ্ট হয়। অর্থাৎ পবিত্রতা নষ্ট হয়।
এখন প্রশ্ন— এই বর্ণপ্রথার ধারণা এলো কীভাবে? ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয় আর্যরা ছিল মধ্য এশিয়ার যাযাবর জাতি। তাঁরা ক্রমেই পূর্বদিকে অগ্রসর হতে হতে সিন্ধু নদ পার হয়ে ভারত উপমহাদেশে প্রবেশ করে। যেহেতু ভারতের তৎকালীন দ্রাবিড়, কোল, ভিল, মুণ্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি জাতি ছিল কৃষিজীবী এবং খাদ্য আহরক, যারা খাদ্য আহরণ অর্থনীতির মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। তাঁদের প্রযুক্তি ছিল অতীব প্রাথমিক পর্যায়ের। অপরদিকে পশুপালন এবং শিকারজীবী আর্যরা ছিল যোদ্ধা জাতি। দীর্ঘকায় অশ্বচারী আর্যরা দ্রুতগতিতে ভারতে প্রবেশ করে অপেক্ষাকৃত খর্বকায় নিম্ন প্রযুক্তির ভারতের আদিবাসীদের সহজে পরাভূত করে দাসে পরিণত করে। এই দাসত্বকে স্থায়িত্ব দান করার জন্য এর একটা সামাজিক ব্যাখ্যা দান করা হল। যার বহিঃপ্রকাশ বর্ণপ্রথা। এটা ইউরোপীয়দের বর্ণবাদের মতোই নিবর্তনমূলক প্রথা। কারণ সাধারণত কোনো ব্রাহ্মণ ক্ষুদ্র-কৃষ্ণকায় হয় না, আবার কোনো শূদ্র দীর্ঘ নাসিকা সংবলিত দীর্ঘদেহী শ্বেতকায় হয় না। যেহেতু আর্যরা এমন অঞ্চল থেকে এসেছিল যেখানে জীবন ছিল সংগ্রামমুখর, গতিময় আর আহার্যের স্বল্পতা।
বহিঃশত্রুর আক্রমণ, চারণভূমির জন্য কিংবা পালিত পশুর নিরাপত্তার জন্য সর্বদাই তাদের যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হতে হত। সংগ্রামী জীবন তাঁদেরকে উচ্চ মেধা এবং কল্পনা শক্তি দিয়েছিল। সেই কারণেই হয়তো সহজ-সরল জীবনযাপনে অভ্যস্ত কৃষিজীবী ভারতীয়দের তাঁরা সহজে পরাভূত করতে পেরেছিল। আর্যরা উপলব্ধি করল এখানে খাদ্যের প্রাচুর্য আছে যার জন্য তাঁদের আজীবন সংগ্রাম করতে হত। তাই চতুর ও বিচক্ষণ আর্যরা বিজিত কৃষিজীবীদের তাঁদের স্বপেশায় নিয়োজিত রেখে উৎপাদনের চাকা সচল রাখল এবং এমন এক কর্মকৌশল উদ্ভাবন করল যাতে করে তাঁরা কখনোই সমাজের উপরিকাঠামোর অংশীদারিত্ব দাবি না করে। ফলে এমন এক অভিনব ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটল, যার মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনের নিশ্চয়তা অটুট থাকল, যার জন্য আর্যদের অহর্নিশি সংগ্রাম করতে হত। আবার সামাজিক শৃঙ্খলা বিধানের দুরূহ কার্যটিও আনায়াসে সমাধান হয়ে গেল, যার জন্য পৃথিবীর প্রায় সব সমাজকে বাড়তি অর্থ এবং শ্রম নিয়োজিত করতে হত। এভাবেই আর্যরা আদিবাসী ভারতীয়দের কার্যত দাসে পরিণত করল।
ঋগবেদের যুগেই যে চারটি বর্ণের উৎপত্তি হয়েছিল তার বীজ বা প্রমাণ পুরুষ সুক্ত (১০/৯০)। সেখানে দ্বাদশ ঋকে আছে পুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ হল, দুই বাহু বা হাত থেকে রাজন্য হল, দুই ঊরু থেকে বৈশ্য হল এবং দুই চরণ বা পা থেকে শূদ্র হল। ঋগবেদের অন্যত্র দুটি মূল ভাগ পাই– আর্য এবং দাস (১০/১০২/৩)। মনে হয় এটি জাতিভিত্তিক (racial) বিভাগ। পরবর্তী সময়ে যখন এই দাসজাতি সমাজের অঙ্গীভূত হয় গেল তখন তাঁরা শূদ্র বলে বর্ণিত হল। অথর্ব বেদে দাস অর্থে শূদ্র শব্দের ব্যবহার হয়েছে (৪/২০/৪)। বৃত্তি বা পেশা অনুসারেই যে বিভাগের ব্যবস্থা হয়েছিল তা বোঝা যায়। অবশ্য তখনও বর্ণ বিভাগ পুরুষানুক্রমিক হয়নি। তার উৎকৃষ্ট প্রমাণ ৯/১১২ সুক্ত। তাতে দেখা যায় একই পরিবারে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন রকম বৃত্তি অবলম্বন করত। সেই পরিবারের একজন স্তোত্রকার, তাঁর পুত্র চিকিৎসক এবং কন্যা যব ভাঙে। যে ঘৃণ্য জাতিভেদ প্রথার অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে আজ ভারতবর্ষ আকুল, ঋগবেদের যুগে কিন্তু এ জাতিভেদ প্রথার সৃষ্টি হয়নি। তখন জাতি বলতে মাত্র দুটি শ্রেণিই বুঝাত– আর্য এবং অনার্য। পরবর্তীকালে শূদ্রদের মতো অনার্য জাতির লোকেরা তাদের ভয় করে চলত বলে অনেকে মনে করেন। আর্য বর্ণের মানুষরা ইন্দ্রের কাছে কী প্রার্থনা করছে একবার দেখা যাক– “হে মেঘবন! নীচ বংশীয় ধন আমাদের প্রদান করো” (৩/৫৩/১৪)। এই বাক্যে অনার্যদের প্রতি বিন্দুমাত্র সমীহ আছে বলে আমার মনে হয় না। যাই হোক, সে সময় কিন্তু বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল বলে মনে হয় না। এটা মুসলমান। আকবর আর হিন্দু রাতপুতদের মধ্যে ভালোবাসার মতোও হতে পারে! তবে লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, ঘৃণা –এসব পরবর্তীকালের সংযোজন।
পরবর্তী ব্রাহ্মণ্যবাদীরা সমাজব্যবস্থাকে কঠোরভাবে চার বর্ণে ভাগে ভাগ করে দিল। ভাগ করে দিল কাজ, কর্তব্য এবং অধিকার।
(১) ব্রাহ্মণ : “অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা/দানং প্রতিগ্ৰহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ।” অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের জন্য তিনি সৃষ্টি করলেন অধ্যাপনা, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগৃহ।
(২) ক্ষত্রিয় : “প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।/ বিষয়েষপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ।” অর্থাৎ ক্ষত্রিয়ের কর্ম লোকরক্ষা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও বিষয়ে অত্যাসক্তির অভাব।
(৩) বৈশ্য : বৈশ্যের কর্ম হল পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, সুদে অর্থ বিনিয়োগ ও কৃষি।
(৪) শূদ্র : প্রভু শূদ্রের একটিমাত্র কর্ম নির্দেশ করলেন। তা হল সকল বর্ণের অসূয়াহীন সেবা করা।
আর কেনই-বা করবে না! সমস্ত শূদ্রদের প্রশ্নহীনভাবে উপরের তিন বর্ণের ফাই-ফরমাশ খাটতেই হবে। এটাই দস্তুর, নিয়তি। কারণ –জাতমাত্রেই ব্রাহ্মণ পৃথিবীতে সকল লোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন এবং সকল সৃষ্ট পদার্থের ধর্মসমূহ রক্ষার জন্য প্রভু হন–
“ব্রাহ্মণণা জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং ধর্মকোষস্য গুপ্তয়ে।”
অথবা– পৃথিবীতে যা কিছু আছে সেই সব ব্রাহ্মণের সম্পত্তি। শ্রেষ্ঠত্ব ও আভিজাত্য হেতু ব্রাহ্মণ এই সবই পাওয়ার যোগ্য–
“সর্বং স্বং ব্রাহ্মণেস্যেদ্যং যৎকিঞ্চিজ্জগতীগতম্।
শ্রৈষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সর্বং বৈ ব্রাহ্মণোহর্হতি।”
কিংবা –ব্রাহ্মণ নিজের অন্নই ভক্ষণ করেন, নিজের বস্ত্র পরিধান করেন এবং নিজের দ্রব্য দান করেন। অন্য লোকেরা যা ভোগ করে, তা ব্রাহ্মণের দয়া হেতু করে।
অপরদিকে শাসক বা রাজা বা ক্ষত্রিয়দেরও প্রভু পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন বিচক্ষণ সমাজপতিরা। মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায় দেখুন— রাজশূন্য এই জগতে চারদিকে ভয়ে (সকলে) প্রচলিত হলে এই সমগ্র (চরাচর জগতের) রক্ষার জন্য ঈশ্বর ইন্দ্র, বায়ু, সূর্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও কুবেরের শাশ্বত অংশ গ্রহণ করে রাজাকে সৃষ্টি করেছিলেন–
“অরাজকে হি লোকেহস্মিন সর্বতো বিদ্যুতে ভয়াৎ।
রক্ষার্থমস্য সর্বস্য রাজানমসৃজৎ প্রভুঃ।
ইন্দ্রানিলমার্কাণামগ্নেশ্চ বরুণস্য চ।
চন্দ্রবিত্তেশয়োশ্চৈব মাত্রা নিত্য শাশ্বতীঃ।”
যেহেতু এই শ্রেষ্ঠ দেবগণের অংশ থেকে রাজার সৃষ্টি হয়েছিল, সেইজন্য তিনি সকল জীবকে তেজে অভিভূত করেন–
“যস্মদেষাং সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভ্যো নৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্বভূতানি তেজস্য।”
অথবা –রাজাকে বালক হলেও মানুষ মনে করে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। ইনি মানুষের রূপে মহান দেবতা —
“বলোহপি নামমন্তব্যো মনুষ্যা ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষা নররূপেণ তিষ্ঠতি।”
এই অধ্যায়ে এ রকম ২২৬টি শ্লোকে ভয় ধরানো বর্ণনা, বিশেষণ এবং নিদানের উল্লেখ আছে।
দেখা যাচ্ছে এঁরা সবাই-ই দেবতা বা সুর, এঁরা ছাড়া বাকি সব দৈত্য বা অসুর। তাই নিয়মনীতিও আলাদা —
“ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্ৰয়ো বৰ্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ।” (১০/৪)
অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের পক্ষে উপনয়ন সংস্কারের বিধান থাকায় এঁরা ‘দ্বিজাতি’ নামে অভিহিত হয়। আর চতুর্থ বর্ণ শূদ্র উপনয়ন সংস্কারবিহীন হওয়ায় দ্বিজাতি নয়, তাঁরা হল ‘একজাতি’। কারণ শূদ্রের পক্ষে উপনয়ন-সংস্কারের বিধান নেই। অতএব অনিবার্যভাবে শূদ্ররা হল নিম্নবর্ণ। ফলে এঁরা ব্রত যজ্ঞ অনুষ্ঠানাদি পালনের যোগ্য হতে পারে না। এছাড়া পঞ্চম কোনো বর্ণ নেই অর্থাৎ ঐ চারটি বর্ণের অতিরিক্ত যাঁরা আছে তাঁরা সকলেই সঙ্করজাতি। হিন্দুধর্মের চারবর্ণের সর্বশেষ ধাপে অবস্থান শূদ্রের। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য– যাঁদের সভ্য ভাষায় বলা হচ্ছে উচ্চবর্ণ বা উঁচু জাত এবং শূদ্রদের বলা হয় নিন্মবর্ণ বা নিচুজাত বা ছোটোজাত।
ডা. ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের মতে মনুর শ্লোকে ‘অনার্য’ শব্দের কুল্লুকভট্ট অর্থ করেছেন ‘শূদ্র’। কিন্তু অনার্য হলেই শূদ্র হয় না। Buehler অনার্য শব্দটির অর্থ করেছেন non-Aryan। এই অর্থ ঠিক নয়। Jones বলেছেন –base-man ও base-women। অনার্য শব্দের অর্থ নীচ, হীন এবং ব্রাহ্মণবিরোধী।
একজন মানুষ মৃত্যু বরণ করলে, মৃত ব্যক্তির পুত্র-কন্যা ও নিকট আত্মীয় স্বজনেরা হিন্দু সমাজের বিধান অনুযায়ী অশৌচ হয়ে যায়। এ জন্য জাতিভেদের নিয়ম অনুসারে ১০-১২-১৫-৩০ দিন অশৌচ পালন শেষে ব্রাহ্মণ দ্বারা মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করে তারপর পবিত্র হতে হয়।
“শুধ্যেদ্বিপ্যো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্য পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যাতি।”
— যাঁরা ১০দিন অশৌচ পালন শেষে ১১দিনে শ্রাদ্ধনুষ্ঠান করে তাঁরা ব্রাহ্মণ, যাঁরা ১২দিন অশৌচ পালন শেষে ১৩ দিনে শ্রাদ্ধনুষ্ঠান করে তাঁরা ক্ষত্রিয়, যাঁরা ১৫দিন অশৌচ পালন শেষে ১৬দিনে শ্রাদ্ধনুষ্ঠান করে তাঁরা বৈশ্য, আর যাঁরা ৩০ দিন অশৌচ পালন শেষে ৩১ দিনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে তাঁরাই শূদ্র। এরকম হাজারো বৈষম্যমূলক নিয়মনীতি শূদ্রদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য, ঘৃণ্য করে তুলেছে। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, মনুসংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত– সর্বত্রই শূদ্রদের অপমানের বিবরণ। প্রতি পদে পদে শূদ্রদের প্রান্তিক করে দিয়েছে, শৃঙ্খলিত করেছে। উদাহরণ দিয়ে প্রবন্ধটি ভারাক্রান্ত করতে চাই না।
বহু বছর আগে একটি মহামূল্য গ্রন্থ পাঠ করেছিলাম। গ্রন্থটি ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি’। গ্রন্থটি সম্ভবত তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে লেখক প্রাচীন ভারতের শূদ্রদের অবস্থান নিয়ে যে সমাজচিত্রটি তুলে ধরেছেন, তা শুনলে চমকে যেতে হয়। টুকরো টুকরো মনে পড়ছে। স্মৃতি থেকে এখানে উল্লেখ করার চেষ্টা করি। তিনি লিখেছিলেন– মুড়া নামের এক নীচ জাতীয় নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। চন্দ্রগুপ্ত আসলে জারজ সন্তান। মৌর্যদের শূদ্র বলে গণ্য হত। ভারতীয় জনশ্রুতিতে চন্দ্রগুপ্তকে শূদ্র বলেই অভিহিত করা হয়েছে। পুরাণেও চন্দ্রগুপ্তের গোষ্ঠীকে শূদ্র বলা হয়েছে। রাজা নন্দকেও প্রজারা পছন্দ করত না। কারণ তিনি ছিলেন নীচকুলোদ্ভব নাপিতের ঔরসজাত। তাই তিনি ঘৃণার যোগ্য।
শেষ নন্দরাজা কিংবা চন্দ্রগুপ্তের ধমনীতে শূদ্ররক্ত প্রবাহিত ছিল কি না তা নিশ্চয় গবেষণার বিষয় হতে পারে। কিন্তু মৌর্যরা যে শূদ্রবংশীয় ছিলেন, তা ভারতীয় লেখকরাই লিখে গেছেন। ব্রাহ্মণদের দ্বারাই মৌর্যরা উৎপাটিত হয়েছিল। শূদ্র তো ছাড়, ক্ষত্রিয়দের পিছনেও ব্রাহ্মণরা আদাজল খেয়ে লেগেছিল। সেইকাল থেকেই ব্রাহ্মণদের উপর ক্ষত্রিয়দের ঘৃণার সূত্রপাত হয়েছিল। ব্রাহ্মণদের উপর ঘৃণার জন্য ক্ষত্রিয়রা পর্যন্ত বৈদিক ধর্ম পরিত্যাগ করেছিল। ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে দীর্ঘ সংগ্রাম এবং জৈন ও বৌদ্ধধর্মে ধর্মান্তর ব্রাহ্মণদের বড়োই বিচলিত করে তুলেছিল। ক্ষত্রিয়ের আধিপত্য ধ্বংস করার জন্য ব্রাহ্মণরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। সেসব কাহিনি আমরা রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণগুলিতে পাই। এইসব গ্রন্থে আমরা দেখতে পাই, ব্রাহ্মণদের ষড়যন্ত্রে কীভাবে ক্ষত্রিয়কুল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। ব্রাহ্মণপ্রবর কৌটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্র’ গ্রন্থে এইসব কার্যের সমর্থন প্রকাশ পেয়েছে। যে সময় ক্ষত্রিয়রা ঘৃণাভরে দলে দলে বৈদিক ধর্ম ত্যাগ করতে থাকল, তখন ধুরন্ধর এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণ নতুন এক অস্ত্র বা পথের সন্ধান করতে থাকল। সেই পাওয়াও গেল। ব্রাহ্মণপ্রবর কৌটিল্য (চাণক্য) শূদ্রদেরকেই অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করলেন। সামশাস্ত্র মতে, আর-এক ব্রাহ্মণপ্রবর ভরদ্বাজ বলেন, সুযোগ পেলে ব্রাহ্মণ মন্ত্রীরা ক্ষত্রিয় শাসন অপসারণ করে ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেতে পারে। কিন্তু বিচক্ষণ কৌটিল্য সেই মত গ্রহণ করলেন না। কৌটিল্য চন্দ্রগুপ্তের মতো অসভ্য’ শূদ্র-সর্দারদের রাজারূপে হাজির করলেন। পুরাণগুলো থেকে জানা যায়, মহাপদ্ম নন্দের পর ক্ষত্রিয়কুল নির্বংশ হয়। এরপর ‘পৃথিবীর রাজারা শূদ্রবংশীয় ছিল’ (বিষ্ণুপুরাণ ৪, ২৪)। সামশাস্ত্রী বলেন– এটা অস্বীকার করা যায় না যে, বিরুদ্ধবাদী ক্ষত্রিয় রাজাদের দ্বারা অত্যাচার ও উৎপীড়নের যন্ত্রণায় বিতারিত হয়ে ব্রাহ্মণরা শূদ্রবংশীয় জংলি সর্দারদের সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। সেই সুযোগে জংলি কৌম দলপতিরা অনেকে আর্যরাষ্ট্রে রাজা হয়ে যান। এইভাবে শূদ্রদের সাহায্য নিয়ে এক ক্ষত্রিয় জাতি ধ্বংস করে অন্য ক্ষত্রিয় জাতির সৃষ্টি করে। সেই সত্যকে একটু ঘুরিয়ে পরশুরামের পৃথিবীকে ২১ বার নিঃক্ষত্রিয় করার কাহিনি উপস্থাপন করা হয়েছে।
বিষ্ণুপুরাণে আমরা পাচ্ছি– “মগধে বিশ্বস্ফটিক নামে একজন রাজা অন্য জাতিদের (উপজাতি) প্রতিষ্ঠিত করবেন। তিনি ক্ষত্রিয়দের নির্বংশ করে জেলে, বর্বর, যদু, পুলিন্দ এবং ব্রাহ্মণদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করবেন। পদ্মবতী, কান্তিপুর ও মথুরাতে নয়জন নাগ জাতি রাজত্ব করবেন। দেবরক্ষিত নামে একজন রাজা সমুদ্রতীরে একটি নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কোশল, ওড়, পুক আভিরেরা এবং শূদ্রেরা সৌরাষ্ট্রে, অবন্তী, সুর, আরবুদ মরুভূমি দখল করবে। শূদ্র, অন্ত্যজ এবং বর্বররা সিন্ধুতীর, দ্বারিকা, চন্দ্রভাগা ও কাশ্মীরে অধীশ্বর রূপে রাজত্ব করবে।”
এখন প্রশ্ন, পুরাণোক্ত এই বিশ্বস্ফটিক (কারও বিশ্বসফানি) কে ছিলেন? এঁর প্রকৃত নাম বাণস্পর। ইনি শক-সম্রাট কনিষ্কের অধীনে বেনারস বা বারাণসী প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি খ্রিস্টীয় ৯০ সাল থেকে ১৩০ সালের মধ্যে রাজত্ব করেছিলেন। তিনি ভারতীয় সমাজকে ব্রাহ্মণশূন্য করেছিলেন। উচ্চশ্রেণির বৈদিকধর্মীদের নামিয়ে নীচ জাতি এবং বিদেশিদের উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। ক্ষত্রিয়দের নির্বংশ করে নতুন শাসকজাতি সৃষ্টি করেছিলেন। কৈবর্ত শ্রেণি থেকে একটি নতুন শাসক অথবা রাজকর্মচারীশ্রেণি সৃষ্টি করেছিলেন। অস্পৃশ্য পচ্চকদের মধ্য থেকেও রাজকর্মচারী সৃষ্টি করেছিলেন। শক, পুলিন্দ জাতির লোক এনে বুন্দেলখণ্ড ও বিহারের মধ্যবর্তী স্থানগুলোতে উপনিবেশ করান। এই বক্তব্য ‘History of India’ গ্রন্থের লেখক শ্ৰীযুক্ত জয়সওয়ালের। জয়সওয়াল লিখেছেন– এই বাণস্পর বংশ এখনও বুন্দেলখণ্ডে আছে, তাঁরা নীচ বংশীয় বলেই গণ্য হয়। রাজপুতদের সঙ্গে তাঁরা বিবাহকার্য করতে পারে না।
এই বিশ্বস্ফটিকই কি ইতিহাসে চন্দ্রগুপ্ত? ঐতিহাসিক ডা. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত অবশ্য এমনই দাবি করেছেন তাঁর গ্রন্থে। যাই হোক, মোদ্দা কথা হল, ব্রাহ্মণদের দাপট ও দৌরাত্ম্য সাময়িক হলেও চূর্ণবিচূর্ণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন বিশ্বস্ফটিক। তাঁর এই মহা-বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ব্রাহ্মণদের পরিকল্পিত বর্ণাশ্রম ধর্ম এবং পুরুষসূক্তের বর্ণগুলির উৎপত্তি ও তাঁদের কর্ম বিষয়ে ব্যবস্থাপদ্ধতি চরমভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়।
বেদোক্ত ‘দস্যু’, ‘দাস’, এবং পরবর্তী সময়ে শূদ্রেরা যখন ভারতের শাসকরূপে উন্নীত হল, তখন ফ্রান্সের মতো পতিতদের উত্থান হয়েছিল বলে স্বীকার করতে হবে। মূলত অর্থনৈতিক বিবিধ ফ্যাক্টরের মধ্যে বৌদ্ধ বনাম ব্রাহ্মণদের তুমুল কলহ ও সংঘর্ষই ছিল শূদ্র উত্থানের পটভূমি।
একদা বিদেশিরা ভাবত ভারতের ব্রাহ্মণসমাজ সারাজীবন ধর্মচর্চা করেই কাটিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মৌর্যযুগের প্রাককালে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র আবিষ্কারের পর পণ্ডিতমহলে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তাঁরা বুঝলেন, কেবল ধর্মচর্চা নয়, ছিল যুদ্ধচর্চাও। তাঁরা রাজনীতি ও বিজ্ঞানের চর্চাও করতেন। এই অর্থশাস্ত্রই মৌর্য সাম্রাজ্যে আইনরূপে গৃহীত হয়েছিল, যার প্রভাব বৈবস্বত মনু। রচিত মনুসংহিতায় ব্যাপকভাবে পড়ে।
কৌটিল্য গান্ধার দেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণ হলেও তিনি কৃষ্ণবর্ণ ও কদাকার ছিলেন। সেই কারণে মহারাজ নন্দ তাঁকে পদে পদে অপমান করতেন। এই অপমানের শোধ তুলতে ব্রাহ্মণপ্রবর কৌটিল্য শূদ্র চন্দ্রগুপ্তের দ্বারা নন্দবংশের ধ্বংসসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। সেই কারণে ব্রাহ্মণদের প্রতি তাঁর অশেষ দুর্বলতা থাকলেও শূদ্রদের জন্যেও কিছুমাত্র প্রসাদের ব্যবস্থা করেছিলেন। আহ্লাদে নয়, তোষণ করতে। শূদ্ৰজাতিদের তোল্লা দিতেই অর্থশাস্ত্রের তৃতীয় খণ্ডে তেরো অধ্যায়ে বলেছেন –যে শূদ্র গোলামরূপে জন্মগ্রহণ করে নাই ও সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, এবং জন্ম দ্বারা যে আর্য (আর্যপ্রাণ); তাহাকে তাহার জাতিরা বিক্রয় করিলে অথবা বন্ধক দিলে তাহারা ১২ পণ শাস্তি পাইবে; বৈশ্যদের এই প্রকার হইলে ২৪ পণ, ক্ষত্রিয়দের ৩৬ পণ, ব্রাহ্মণদের ৪৮…ম্লেচ্ছদের মধ্যে এই প্রকার কার্য দোষবহ বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু কোনো আর্য গোলামে পরিণত হইতে পারে না।
কৌটিল্য আরও বলছেন –“যে নিজেকে গোলামরূপে বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছে এরূপ ব্যক্তির পুত্র একজন ‘আর্য হইবে।”(১৬) “যে পরিমাণ অর্থের জন্য একজন গোলামে পরিণত হইয়াছে, সেই অর্থ প্রত্যার্পণ করিলে সেই গোলাম পুনঃ তাহার ‘আর্যত্ব’ ফিরিয়া পাইবে।” (১৭) কৌটিল্য ব্রাহ্মণদের শূদ্রা নারীকে গ্রহণ বা বিবাহের অনুমতিও দিয়েছিলেন।
আমরা কৌটিল্যের ‘সংবিধান’ থেকে যে তথ্য পেলাম, তা হল, শূদ্রদের ‘আর্যত্ব’ প্রাপ্তি। আর্য’ শব্দটি এখানে নরতত্ত্ববাচক নয়, এটি রাজনীতিবাচক বলেই প্রতীত হয়। অতএব একথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, মৌর্য সাম্রাজ্যের স্বাধীন বা মুক্ত প্রজারা সকলেই ‘আর্য’ বলে গণ্য হয়েছিল। অথচ শূদ্র-উত্থান তথা কৌটিল্যের প্রবেশের আগে ব্রাহ্মণদের রচিত গ্রন্থগুলি আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদেরই ‘আর্য’ হিসাবে পাই। আর এই বেনিফিটটা শূদ্ররা পায় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সংঘর্ষের ফলেই। যদিও বেনিফিটটা ছিল সাময়িক।
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের মধ্যে সংঘর্ষ কতটা তীব্র ছিল সেটা আমরা রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলি নির্মোহ বিশ্লেষণ করলেই পেয়ে যাব। রামায়ণে আমরা দেখতে পাই ক্ষত্রিয়দের ‘শিখণ্ডী’ করে ব্রাহ্মণগোষ্ঠী অনার্যদের নির্বংশ করেছে। এ বিষয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমার ‘যুক্তিবাদীর চোখে রাম ও রামায়ণ’ গ্রন্থে। তাই রামায়ণের ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণদের সংঘাতের কাহিনি এখানে। আলোচনা করছি না। মহাভারতেও আমরা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের সংঘাতের চিত্র পাই। সেখানেও ব্রাহ্মণগোষ্ঠী ক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয় লেলিয়ে ক্ষত্রিয় ধ্বংস করেছে। একই সঙ্গে যদুবংশও ধ্বংস করেছে। সে যুগে যখন ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়রা পরস্পরের প্রতি ক্ষমতার দ্বন্দ্বে যুযুধান, তখন জমদগ্নিরাম ব্রাহ্মণদের নিয়ে একটি সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলেন। এই বাহিনীকে ব্যবহার করে পরশুরাম একুশবার ক্ষত্রিয় ধ্বংস করেছেন। মহর্ষি ভৃগুর (পরশুরামের প্রপিতামহ) বাক্যানুযায়ী পরশুরাম বৃত্তিতে ক্ষত্রিয় হয়েছিলেন। তাই জগতে তিনিই প্রথম ব্রাহ্মণ যোদ্ধা। পরশুরামের মা রেণুকা ছিলেন অযোধ্যার সূর্যবংশের মেয়ে। এই বংশেই রামচন্দ্রের জন্ম হয়। জমদগ্নির ঔরসে রেণুকার গর্ভে পাঁচ পুত্রের মধ্যে পরশুরাম ছিলেন কনিষ্ঠ। একবার চিত্ররথ নামে এক রাজাকে সস্ত্রীক জলবিহার করতে দেখে রেণুকা কামার্ত হয়ে পড়েন। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সেই দৃশ্য অবলোকন করেন জমদগ্নি। এই অপরাধে স্ত্রীকে শাস্তি দিতে পাঁচ পুত্রকে আহ্বান করলেন। মাকে হত্যা করতে কোনো পুত্র রাজি না-হলেও কনিষ্ঠ পুত্র পরশুরাম রাজি হয়ে যান এবং পিতার আদেশে কুঠারের আঘাতে মায়ের শিরচ্ছেদ করেন। তবে মাতৃহত্যাজনিত পাপে তাঁর হাতের কুঠার হাতেই সংযুক্ত হয়ে যায়। অপরদিকে পুত্রের মাতৃহত্যাজনিত কর্মে খুশি হয়ে পিতা জমদগ্নি তাঁকে বর প্রার্থনা করতে বলেন এবং অখুশি হয়ে বাকি পুত্রদের অভিশাপ দেন। বর হিসাবে পরশুরাম পিতার কাছ থেকে মায়ের পুনর্জন্ম, মাতৃহত্যাজনিত পাপ ও মাতৃহত্যার স্মৃতি বিস্মৃত হওয়া, ভাইদের জড়ত্ব মুক্তি, নিজের দীর্ঘায়ু এবং অজেয়ত্ব প্রার্থনা করেন। জমদগ্নি তাঁকে সবকটি বরই প্রদান করেন। ব্ৰহ্মকুণ্ডে স্নান করার পর হাত থেকে কুঠার বিচ্ছিন্ন হয়েছিল পরশুরামের। হৈহয়রাজ কীর্তবীর্য জমদগ্নির হোমধেনুর গোবৎস বহন করেছিলেন বলে পরশুরাম তাঁকে হত্যা করেছিলেন। কীর্তবীর্যের পুত্ররা প্রতিশোধ নিতে আশ্রমে এসে তপস্যারত জমদগ্নিকে হত্যা করে। ক্ষুব্ধ পরশুরাম একাই কীর্তবীর্যের সব পুত্রকে হত্যা করেন। এরপর তিনি একুশবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করেছিলেন। তিনি ক্ষত্রিয়দের রক্ত দিয়ে সমস্ত পঞ্চক প্রদেশের পাঁচটি হ্রদ পূর্ণ করেন। (সমস্ত পঞ্চকোপাধ্যান– দ্বিতীয় অধ্যায়– আদিপর্ব, মহাভারত) শেষে পিতামহ ঋচিকের অনুরোধে ক্ষত্রিয় হত্যালীলা বন্ধ করেন পরশুরাম। ক্ষত্রিয়রা পরাভূত হন ব্রাহ্মণদের সশস্ত্র বাহিনীর হাতে।
‘বিদুর’ গ্রন্থে লেখক মিহির সেনগুপ্ত লিখেছেন– ক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে ব্রাহ্মণরা বৈশ্য প্রভৃতি বর্ণের সাহায্যও কখনো-কখনো গ্রহণ করেছিল এবং তথাপি পরাজিতও হয়েছিলেন। সে বোধহয় পরশুরামের আবির্ভাবের আগেকার কথা হবে। জামদগ্ন্যরাম যখন ক্ষত্রিয়দের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের নেতৃত্ব দিতে শুরু করেননি, তখন তাঁরা নাকি বৈশ্য এবং শূদ্রদেরও সহায়তা নিয়ে ক্ষত্রিয়দের কাছে বারবার পরাজিত হচ্ছিলেন। মিহির সেনগুপ্ত আরও লিখেছেন– যুদ্ধবিরতিকালীন সাময়িক শান্তির সময়ে ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়দের জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁরা কেন বিজয়ী হতে পারছেন না! ক্ষত্রিয়রা তখন বলেছিলেন যে, এক অখণ্ড নেতৃত্বের অধীনে সংগ্রাম না করলে বিজয় লাভ করা যায় না। আপনারা যে যাঁর বিচারমতো চলতে চান। তাই কখনোই বিজয়লাভ করতে পারেন না। অতঃপর জামদগ্ন্যরামকে ব্রাহ্মণরা তাঁদের অখণ্ড নেতা হিসাবে নির্বাচন করার পরই তাঁরা জয়লাভ করতে শুরু করে। তার পরবর্তী দীর্ঘকাল এই পরশুরামের অনুগামী ব্রাহ্মণেরা শস্ত্রশিক্ষা বিষয়ে সবিশেষ পারদর্শিতা দেখিয়ে আসছিলেন। এঁদের পরবর্তী সব দলপতিকেই এঁরা ‘পরশুরাম’ নামে অভিহিত করে থাকেন। পরশুরাম’ নামটি একদা তাঁদের গোত্ৰনাম হয় এবং গোত্ৰাধিপতি এই নামেই পরিচিত হতে থাকেন। যখন ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণদের বৃত্তির কোনো নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট বিভাগ ছিল না, তখন এইসব পরশুরামেরা বহুবার ক্ষত্রিয়দের নিঃশেষ করার সংগ্রামে জয়ী হয়েছেন।
বস্তুত ক্ষমতা কুক্ষিগত করার কারণেই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের এই দীর্ঘকালীন বিরোধ। এরপর ব্রাহ্মণেরা বিধ্বংসী ও নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। সূক্ষ্ম বুদ্ধিপ্রয়োগে শাসকের আসনে না-বসলেও ক্ষত্রিয়দের পুতুলে পরিণত করে ব্রাহ্মণরাই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠলেন। এমনকি সামরিক বিভাগটিও ব্রাহ্মণরা নিজেদের দখলে রেখেছিলেন। বিশ্বামিত্র, বশিষ্ট, দুর্বাসা, দ্রোণাচার্য, মার্কণ্ডেয়, অগস্ত্য প্রমুখ দোর্দণ্ডপ্রতাপ ব্রাহ্মণেরা ছিলেন সামরিক শক্তির আধার। বিশাল অস্ত্রভাণ্ডার ছিল তাঁদের। যুদ্ধকালে এইসব ব্রাহ্মণদের কাছ থেকেই অস্ত্র সংগ্রহ করতে হত ক্ষত্রিয় যোদ্ধাদের। প্রাচীন যুগে ব্রাহ্মণরাই ছিলেন মূল ক্রীড়ক, ক্ষত্রিয়রা ছিলেন ক্রীড়নক মাত্র।
মৌর্যযুগের কৌটিল্য শূদ্রদের ঢেলে অধিকার দিয়েছে, একথা ভাবা মূর্খামি। ব্রাহ্মণদের আধিপত্য ঘষালো আনা অক্ষুণ্ণ রেখেই শূদ্রদের যৎসামান্য দেওয়া হয়েছে। ভিক্ষার দান! না-হলে নিজে ব্রাহ্মণ হয়েও কীভাবে শূদ্রদের ঘি-মাখন খাওয়ার ব্যবস্থা করে! কাজ হাসিল করে পিছনে পদাঘাত। কৌটিল্য শূদ্রদের এতই মঙ্গল চেয়েছিলেন যদি, তাহলে শূদ্র-শাসনকালেই শূদ্ররা পূর্ণমুক্তি পেল না কেন? মৌর্য সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি হয় চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোকের রাজত্বকালে। যদিও চন্দ্রগুপ্তকে সম্রাট করে ব্রাহ্মণরা নিজেদের আধিপত্য একচেটিয়া করতে যথাসম্ভব চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে ব্রাহ্মণদের সেই আশায় ছাই ঢেলে দেয়। অশোক বৌদ্ধ হয়েই অনুশাসন যজ্ঞে জীবহিংসা নিষিদ্ধ করে দেন। এই অনুশাসন অবশ্যই ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে গেল। কারণ এই অনুশাসন একজন শূদ্ররাজার হুকুম। অশোক বারবার মনে করিয়ে দিতেন –যাঁরা পূর্বে পৃথিবীতে দেবতা বলে মান্য হতেন, তাঁদের তিনি মিথ্যা দেবতায় পরিণত করে দিয়েছেন। বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন– যাঁরা ‘ভূদেব’ (ব্রাহ্মণ) বলে সম্মান ও পুজো পেত, তাঁদেরও তিনি মিথ্যা বলে প্রমাণ করে দিয়েছেন। অতঃপর অশোক ধৰ্ম্ম-মহাপাত্র, অর্থাৎ নীতি পর্যবেক্ষণের নিযুক্তি করে ব্রাহ্মণদের অধিকার ও সুবিধাভোগের উপর হস্তক্ষেপ করেন।
ব্রাহ্মণদের অনুশাসনে শূদ্ররা যেসব নির্যাতন ভোগ করত, অশোক তা সংশোধন করেন। তিনি জাতি, বর্ণ ও ধর্মে সাম্য স্থাপনে সচেষ্ট হন। এই সাম্যবাদ ব্রাহ্মণদের স্বার্থে কুঠারাঘাত করে। তাঁদের কাছে খুবই অসহ্য ও আপত্তিজনক মনে হয়েছিল। কারণ এই সাম্যবাদে ব্রাহ্মণেরা ‘অবধ্য ও মৃত্যুদণ্ডের অতীত’ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হন। ব্রাহ্মণেরা এ সময়কালে খাপে খাপ হয়ে গিয়েছিলেন। একদম কোণঠাসা অবস্থা। তথাপি কোণঠাসা হয়েছিলেন বলে তাঁরা হাত গুটিয়ে বসে থাকননি। অপেক্ষা করছিলেন একটা সুযোগের জন্য। খুঁজছিলেন কৌশল।
মৌর্যশাসনের সময়ই পাটলিপুত্র নগরে রাজসৈন্যের কুচকাওয়াজের সময়। ব্রাহ্মণ-সেনাপতি পুষ্যমিত্র রাজাকে হত্যা করে সিংহাসন দখল করে নেয়। বলা যায় ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীলতা এই সময় থেকেই শুরু হয়ে গেল। এ সময় থেকেই বৌদ্ধশাসন ভেঙে দিয়ে ব্রাহ্মণ আধিপত্য কায়েম হয়ে যায়। এই সময়েই তথাকথিত মানবধর্মশাস্ত্র মনুসংহিতা বা মনুস্মৃতি পুনঃসংকলিত (নবরূপে) প্রকাশ্যে এলো। জয়সওয়াল ও জলির মতে, এই গ্রন্থ পাটলিপুত্রের জনৈক ব্রাহ্মণ সুমতী ভার্গব কর্তৃক রচিত হয়। গ্রন্থটি রচনার সময় পুষ্যমিত্রকে মাথায় রেখে কী প্রকার অবস্থায় অথবা কী প্রকার চরিত্রের রাজা বিনষ্ট হয়, তা বর্ণিত হয়েছে। মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায় জুড়ে রাজা কে, রাজা কী, রাজা কেন, রাজা কীভাবে, রাজা কী করবে, কী করবে না –তার পুঙ্খানুপুঙ্খ নীতিনির্দেশ লিখিত হয়েছে। কারণ রাজা পুষ্যমিত্র ছিলেন একজন রাজহন্তা। বস্তুত ভার্গবই শূদ্র-বিদ্বেষপূর্ণ এবং পুষ্যমিত্রের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ মনুসংহিতায় বিষবৃক্ষ রোপণ করে দিলেন।
এই স্মৃতিগ্রন্থেই ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে এবং অবশ্যই শূদ্রদের প্রতি কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। শূদ্রদের ঘৃণ্যতর করা হয়েছে। আদি মনুসংহিতায় বা স্মৃতি সমূহে শূদ্রদের প্রতি এত বিদ্বেষ ছিল না। মনুর মতে– “শূদ্র বিচারকের পদ পেতে পারে না।” (৮/২০) “যে রাজ্য শূদ্রবহুল, নাস্তিকতাক্রান্ত এবং দ্বিজশূন্য –সেই রাজ্য অচিরেই দুর্ভিক্ষ ও বহুবিধ ব্যাধিপ্রপীড়িত হয়ে বিনষ্ট হয়ে থাকে।” (৮/২২) বাস্তবিকই এই গ্রন্থ থেকে অশোকের দণ্ড সমতাগুলি বাতিল করা হয়েছে। উপরন্তু বলা হয়েছে, উচ্চশ্রেণির মানুষরা যদি নীচশ্রেণির মানুষদের উপর অত্যাচার করলে দণ্ড কম হবে। কিন্তু নীচশ্রেণির মানুষরা যদি উচ্চবর্ণের উপর অত্যাচার করে তাহলে তাঁর দণ্ড অধিক হবে। “দর্পের সঙ্গে শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে ধর্মোপদেশ দেয়, তাহলে রাজা তাঁর মুখে ও কানে গরম তেল ঢেলে দেবে।” (৮/২৭২) শূদ্র যদি শ্রেষ্ঠ জাতির প্রতি কোনো প্রকার হিংসামূলক কাজ করে তাহলে সেই অপরাধের জন্য হাত বা পা, নিতম্ব কর্তন করে দেবে, অথবা ঠোঁট দুটি ছেদন করে দেওয়া হবে।” (৮/২৭৯-২৮৩) মনু নির্দেশ দিয়েছেন– ব্রাহ্মণ বিশ্রদ্ধচিত্তে দাস-শূদ্রের ধন সম্পদ আত্মসাৎ করতে পারেন। কোনো জিনিসই তাঁর নিজস্ব নয়। তাঁর সমুদয় অর্থই ভর্তৃহার্য। (৮/৪১৭) এখানেই শেষ নয়, নিজেদের বন্দোবস্তও করিয়ে রাখেন। বলছেন –“রাজা অর্থাভাবে মরণাপন্ন হলেও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের কাছ কখনো কর গ্রহণ করবে না।” (৭/১৩৩) সেই মনুর নীতি আজও অব্যাহত। আজও মন্দিরের রোজগার আয়কর নেওয়া হয় না। মন্দিরের আয় নিষ্কর। আয়কর দফতরকে কোনো রিটার্ন জমা দিতে হয় না। অথচ ভাবুন তো কী বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ মন্দিরগুলো আয় করে। কষ্ট করে ভাবার দরকার নেই। আসুন দেখে নিই মন্দিরের রাজগার।
ভারতের সবচেয়ে সম্পদশালী মন্দিরটি হল কেরালায়। মন্দিরটির নাম পদ্মনাভস্বামী। এদের বার্ষিক আয় কত জানা যায় না। তবে এখানের সম্পদের মূল্য প্রায় ১১ লাখ কোটি টাকা।
তালিকার দ্বিতীয় নাম্বারে রয়েছে তিরুপতি বালাজি মন্দির। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী দেবতা। মন্দির চত্বরের মূল মন্দিরটি সোনা দিয়ে মোড়া। মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রদীপের আলোয় দেবদর্শন। কালো বিশাল মূর্তির মাঝে সোনার প্রলেপ। বছরভর ভিড় লেগেই থাকে এই বিশ্ববিখ্যাত মন্দিরে। হতদরিদ্র থেকে কোটিপতি, অভিনেতা থেকে মেগাস্টার, রাজনীতিবিদ থেকে মন্ত্রীসান্ত্রী, এমনকি দেশের বাইরের কূটনীতিবিদরাও তিরুপতি মন্দিরে আসেন। বছরভর প্রচুর মানুষের আনাগোনা লেগেই থাকে। প্রতিদিন প্রায় ৭০ হাজার ভক্ত এখানে উপাসনা করতে আসেন। উৎসব ও পার্বণে এই সংখ্যা ৫ লাখ ছাড়িয়ে যায়। এই মন্দিরের বার্ষিক আয় প্রায় সাড়ে ৭ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা আয় হয় দান থেকে। দর্শনার্থীদের কাছে টিকিট বিক্রি করে আয় হয় প্রায় ৩০০ কোটি টাকা। বাকিটা আসে বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ থেকে। আছে ডোনেশন। এই মন্দিরে ২০ টন সোনা ও হিরার গহনা আছে। ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুমালা তিরুপতি ভেঙ্কটেশ্বর মন্দিরে শুধু সোনা রয়েছে ৩০০০ কেজি, আর তাদের ঘোষিত সম্পত্তি রয়েছে ৫০,০০০ কোটি টাকা।
জম্মু ও কাশ্মীরের বিষ্ণুদেবী মন্দির সবচেয়ে পুরাতন মন্দির। প্রতিবছর আনুমানিক ৮০ লাখ ভক্ত এখানে উপাসনা করতে আসেন। যে সংখ্যাটি বালাজি মন্দিরের পরেই। এই মন্দিরের আয় প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। অন্য মন্দিরগুলোর মতোই এখানেও থাকার বন্দোবস্ত আছে।
সম্পদের দিক থেকে চার নাম্বারে পাঞ্জাবের অমৃতসরের গোল্ডেন টেম্পল বা সোনালি মন্দির। শিখ গুরু অর্জুন ষোড়শ শতকে এই মন্দির নির্মাণ করেন। প্রতিদিন প্রায় ৪০ হাজার ভক্ত এখানে আসেন। কাঠ, সোনা আর রূপার কারুকাজে পুরো মন্দির দৃষ্টি কাড়ে। এই মন্দিরের বার্ষিক আয় সুনির্দিষ্টভাবে জানা যায়নি।
মুম্বাইয়ের গণপতি মন্দির হল দেবতা গণেশের মন্দির। অষ্টাদশ শতকে এই মন্দির তৈরি করা হয়েছে। গণেশের মূর্তির মুকুটে সাড়ে তিন কেজি সোনা ব্যবহার করা হয়েছে। দিনে গড়ে প্রায় লাখ খানেক ভক্ত গণেশকে একনজর দেখতে এখানে আসেন। মুম্বাইতে হওয়ার কারণে বলিউডের নামিদামি তারকারা এখানে আসেন। তারা মুক্তহস্তে দান করেন। ফলে সবমিলেয়ে বছরে আড়াই থেকে তিন হাজার কোটি টাকা আয় করে এই মন্দির।
মুম্বাই শহরের প্রান্তে আর-একটি মন্দির আছে সাঁইবাবা মন্দির। প্রতিবছর কয়েক লাখ দর্শনার্থী এখানে আসেন। এই মন্দির দান থেকে প্রতিবছর আয় করে প্রায় ৫০০ কোটি টাকা।
যাই হোক, ভারতীয় শ্রেণিগুলি যত বনিয়াদি স্বার্থ বিবর্তিত করে নিজেদের স্থানুবৎ অচল করতে লাগল ততই উচ্চশ্রেণির রক্তের বিশুদ্ধতা, জন্মের পবিত্রতা, আচার-ব্যবহারের নানাপ্রকারের বিভিন্নতা ও দাবি উদ্ভূত হতে থাকল। পরিশেষে এলো Divine Right of King। ভারতীয় সমাজ প্রবেশ করল সামন্ততান্ত্রিক যুগে। মানবধর্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ও শূদ্র এবং পতিতদের প্রতি বিশেষ কঠোর ব্যবস্থা দেখে জয়সওয়ালের অনুমান সত্য বলে মনে হয় যে, মৌর্য সাম্রাজ্য ধ্বংস হওয়ার পর ব্রাহ্মণাধিপত্যের সময় ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে মনুসংহিতা তৎসহ বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্র রচিত হল। পুষ্যমিত্রের রাজত্বাধীন রাষ্ট্রে ব্রাহ্মণাধিপত্যের প্রথম যুগ বলা হয়। রাষ্ট্রীয় আইন-অনুশাসনও তখন সেই শ্রেণির স্বার্থ-সুবিধা অনুসারেই সৃষ্টি হয়।
মৌর্যযুগ অবসানের পর ব্রাহ্মণরা ‘অবধ্য’ ঘোষিত হলেও মৌর্যযুগে বা তারও আগে ব্রাহ্মণ বধ্যই ছিল। অনেকে মনে করেন অশোকের সমদণ্ডনীতিতেই ব্রাহ্মণরা প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে পড়ল। এর ফলে ব্রাহ্মণ-বিদ্রোহে মৌর্য সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। বাস্তবিক এ তথ্য সত্য নয়। পূর্বে স্থলবিশেষে ব্রাহ্মণদেরও মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। মহাভারতে যেমন ব্রাহ্মণদের মৃত্যুদণ্ড ছিল, তেমনই বৃহদারণ্যক উপনিষদেও দেখতে পাই জনৈক ব্রাহ্মণ তার্কিক যাজ্ঞবন্ধ্যের প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারায় মুণ্ডহীন হয়েছিল। পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে বর্ণিত আছে, মনিবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার করলে পুরোহিতেরও মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। তবে এগুলো ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের শ্রেণি-সংঘাতের পরিচায়ক। অর্থশাস্ত্রেও আমরা পাচ্ছি, বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে ব্রাহ্মণকে জলে ডুবিয়ে মারার নির্দেশ। ব্রাহ্মণপ্রবর কৌটিল্য মৌর্যসাম্রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন। কাজেই ব্রাহ্মণের বধ্যতা মেনে নিতে হয়েছিল। ব্রাহ্মণদের অকথ্য অত্যাচারে সমাজের বেশিরভাগ নীচজাতীয় মানুষজন বৌদ্ধধর্মে চলে যাচ্ছিল। এসময় কৌটিল্যের পক্ষে শূদ্রদের ‘আর্যত্ব’ না। দিয়ে আর কোনো উপায় ছিল না। অধিকাংশ মানুষ তখন ভেরীঘোষ অপেক্ষা বুদ্ধের ধর্মঘোষ শ্রবণ করাই শ্রেষ্ঠ মনে করেছিলেন। ধৰ্ম্মঘোষ শ্রবণ করা মানেই পুরোহিত ডেকে যাগযজ্ঞ করার মানুষজনও আর থাকছিল না। বৌদ্ধধর্ম ও শূদ্ৰাধিপত্যের ফলে ব্রাহ্মণদের বনিয়াদি স্বার্থে ব্যাপক আঘাত লাগে। সেই আঘাতেই ব্রাহ্মণপ্রবর ক্ষেপে ওঠেন। প্রাচীন মনুসংহিতা গ্রন্থটি চালাচালি করে নব সংযোজন করলেন। মনুর নামেই মনুসংহিতা প্রয়োগ হতে থাকল। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর মনুশাসন শূদ্রদের দাবিয়ে রাখার জন্য কঠোর বিধিনিষেধ প্রণয়ন করলেন।
শাস্ত্রসমূহ ঘোষণা দিল –সব ধরনের পাপের পাপী হলেও ব্রাহ্মণকে কখনোই হত্যা করা যাবে না (মনুসংহিতা, ৮/৩৮০)। রাজাকে নির্দেশ দেওয়া হল– ক্রীত হোক বা না হোক, শূদ্রকে দিয়ে সমস্ত রকমের দাস্যকর্ম করিয়ে নেবেন। কারণ বিধাতা শূদ্রদের দাস্যকর্ম করানোর জন্যেই সৃষ্টি করেছেন। শূদ্র প্রভুমুক্ত হলেও দাসত্বমুক্ত হয় না। দাস্যকর্ম তাঁর জন্য স্বাভাবিক। অতএব কার সাধ্যি শূদ্রদের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবে? এইভাবেই ব্রাহ্মণ্যধর্মের ব্রাহ্মণ্যবাদীরা কৌশলে শূদ্রদের ‘চিরঅভিশপ্ত থেকে যাওয়ার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়ে গেল। শূদ্রদের প্রতি ঘৃণা এমন পর্যায়ে চলে গেল যে, শূদ্রের কেউ উচ্চবর্ণের দাওয়ায় বসলে সে উঠার পর গোবরজল দিয়ে ধুয়ে ফেলা হয় শূদ্রের ছায়া মাড়ালে বা শূদ্র ছুঁয়ে দিলে উচ্চবর্ণের মানুষরা স্নান করে শুদ্ধ বা পবিত্র হত। উচ্চবর্ণের সামনে দিয়ে শূদ্রকে কোমর ভেঙে পাশ কাটাতে হবে। উচ্চবর্ণের সামনে ছাতা মাথায় দেওয়া যাবে না, কখনোই পায়ে জুতো পরা যাবে না, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ঊর্ধ্বাঙ্গে কোনো কাপড় রাখতে পারবে না ইত্যাদি নানাবিধ অবমাননাকর সমাজব্যবস্থা প্রচলন হল।
ব্রাহ্মণ রাজা হতে পারে। ব্রাহ্মণ দেবতাও হতে পারে। কিন্তু শূদ্র দাস ছাড়া কিছুই হতে পারে না। ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী বৌদ্ধ ও শূদ্রদের প্রতি এইভাবেই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল ব্রাহ্মণ্যবাদীরা। মৌর্যরাও ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়ায় মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন হল। শুরু হল ব্রাহ্মণ্যাধিপত্যের প্রথম যুগ, তা হল পুষ্যমিত্রের রাজত্বাধীন রাষ্ট্রেই। এই সময় সুঙ্গ, কম্ব বংশ মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে উত্তর ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার লাভ করে। পরে দক্ষিণ ভারতে অন্ধ্র, শতবাহন বংশ প্রভূত্ব শুরু করে।
এ সময় দক্ষিণ ভারত উপমহাদেশে এক রাজশক্তির উত্থান হয়। এঁদের অন্ধ্র বা অন্ধ্রভৃত্য বলা বলা হত। মনু তাঁর স্মৃতিগ্রন্থে মেদ, চণ্ডালের মতো গোষ্ঠীকে পতিত বলেছেন। যদিও অন্ধ্রভৃত্য শতবাহন বংশ নিজেদেরকে ব্রাহ্মণ বলত। এই বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠাতা সিরি সতকর্ণি গোতমিপুত্ত নিজেকে ‘একবীর’ ও ‘একব্রাহ্মণ’ বলতেন। ইনি ব্রাহ্মণ্যত্বের ঠেলায় ক্ষত্রিয়দের অহংকার নষ্ট করে দেন। দ্বিজদের স্বার্থোন্নতি সাধন করে চতুর্বর্ণের মিশ্রণ বন্ধ করে দিয়েছিলেন।
অতএব যে শ্রেণির হাতে শাসনযন্ত্র থাকবে রাষ্ট্রের আইন-অনুশাসন ইত্যাদি ব্যবস্থাপত্রও সেই শ্রেণির স্বার্থ ও সুবিধা অনুসারেই সৃষ্ট তথা বিধিবদ্ধ হয়। আজও তার অন্যথা হয় না। অতএব রাজবংশের পরিবর্তন হলেও শাসন পদ্ধতির তেমন কোনো পরিবর্তন হত না। তথাকথিত ধর্মগ্রন্থগুলি তো আদতে শাসনগ্রন্থ বা আইনগ্রন্থই। প্রাচীন রাষ্ট্রধারণায় ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা শাসিত হলেও আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মীয় অনুশাসন তেমন অনুসরণ করা হয় না। তবে সামাজিক অনুশাসনে আজও ধর্মীয় অনুশাসনের প্রভাব আছে। পুরোহিততন্ত্র সেই অনুশাসন চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মৌর্যযুগের অবসানের পরপরই ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের অস্ত্র হিসাবে শাস্ত্র-সংহিতা পুরাণাদি রচিত হল। এইসব গ্রন্থগুলি পাঠ করেই অনুধাবন করা যায় ব্রাহ্মণদের মূল লক্ষ্য সমাজের চার শ্রেণি– ব্রাহ্মণ, রাজা বা ক্ষত্রিয়, নারী ও শূদ্র। এই চার শ্রেণির জন্য ব্রাহ্মণগণ উদয়াস্ত পরিশ্রম করে অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে ফেলেছেন, যা হিন্দুসমাজে সম লাভ করেছে। ঐতিহাসিক জয়সওয়াল বলেন, অন্ধ্ররাজাদের সমসাময়িককালে উত্তর ভারতেই যাজ্ঞবল্ক্যর সংহিতা রচিত হয়। যাজ্ঞবল্ক্য শতবাহন বংশের রাজত্বকালের সমসাময়িক ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর সংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ২৭৩ নম্বর নির্দেশিকায় বৌদ্ধভিক্ষুর বিরুদ্ধে বিষ উগড়ে দিয়েছেন। তিনি সেই নির্দেশিকায় বলেছেন –“হরিদ্রা রঙের কাপড় পরিধানকারী ব্যক্তিগণ অশুভ-দর্শন”। শূদ্রদের বিরুদ্ধে বলছেন– “দ্বিজজাতিদের শূদ্রা স্ত্রীলোক গ্রহণ নিষিদ্ধ। শূদ্র কেবল নিজ জাতির মধ্যে বিবাহ করবে। কারণ প্রতিলোম বিবাহের সন্তানেরা ‘অসৎ’ এবং অনুলোম বিবাহের সন্তানেরা ‘সৎ’ বলে বিবেচিত। ভারতে যে ‘মিতাক্ষরা’ আইন, তা যাজ্ঞবন্ধ্যের সংহিতার উপরই তার ভিত্তি স্থাপিত, যা আজও ভারতে বিদ্যমান। অথচ ব্রাহ্মণ্যবাদীদের শিরোমণি তথা আরএসএসের প্রতিষ্ঠাতা গোলওয়ালকর কী বলছে পড়ন– “শূদ্র মহিলাদের প্রথম সন্তান ব্রাহ্মণ ঔরসজাত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাঁর বিবাহ যাঁর সঙ্গেই হোক না কেন। এতে ব্রাহ্মণ জাতের গুন নিচু জাতের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়” (অর্গানাইজার, ১৯৬১)।
ব্রাহ্মণ্যযুগের পর পুনরায় বৈদেশিক আক্রমণ হল উপমহাদেশে প্রবেশ করে বর্বর শক জাতি। এরা ইরানীয় জাতি হলেও ভারত উপমহাদেশে প্রবেশ করে ভারতীয় সভ্যতা ও ভারতীয় ধর্ম গ্রহণ করে। এরপর মধ্য এশিয়া থেকে কুষাণরা ভারতে প্রবেশ করে শকদের স্থান দখল করে নেয়। তবে কনিষ্করা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম (এ সময় হিন্দু নামে ধর্ম ছিল না। সেইসময়কার কোনো গ্রন্থে এই ধর্মের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।) প্রত্যখ্যান করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। এ সময় ধর্মাচরণে ও সমাজে ব্যাপক ওলোটপালোট লক্ষ করা যায়। এই সময়েই শৈবধর্ম, মহাযান, সূর্যপুজো ও কৃষ্ণের উপাসক সম্প্রদায়ের উত্থান হয়।
বিদেশি তথা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দ্বারা কুষাণরা চিরকাল বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। কুষাণ ক্ষত্রপরা ভারতীয় নাম ও ধর্ম গ্রহণ করলেও গুপ্তসম্রাটদের দাপটে সমূলে উৎপাটিত হয়। কুষাণরা ব্রাহ্মণদের অবিশ্বাস করতেন। সেইজন্যেই কুষাণ রাজারা শূদ্ৰজাতিদের মধ্য থেকে নিজেদের কর্মচারী নিয়োগ করতেন। এ সময়েই বৌদ্ধপণ্ডিত অশ্বঘোষ বলেছেন– “ব্রাহ্মণদের আর শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করার কোনো কারণ নেই। কারণ শূদ্ররা এখন ব্রাহ্মণদের সমান পণ্ডিত হয়েছে। এক্ষণে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র সমান” (বজ্ৰচ্ছেদিকা)। বস্তুত বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রচারের সময় থেকেই ভারতের ইতিহাসে ‘পতিত’ শ্রেণির পুনরুত্থান হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদ-বিরোধী ধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মণশ্রেণির এত বিরোধ ও সংঘর্ষ ছিল যে, সমাজের নিম্নস্তরের শ্রেণি তৎসহ পতিত শ্রেণিরা অন্য নতুন ধর্ম গ্রহণ করে উচ্চবর্ণের উৎপীড়ন ও শোষণনীতির কবল থেকে উদ্ধার পেতে চাইছিলেন। প্রথম দিকে বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে এবং ইসলাম ধর্মে ধর্ম গ্রহণ করে মুক্তির পথ খুঁজে নেয়। অসংখ্য নিম্নবর্গীয় হিন্দুও খ্রিস্টধর্মে চলে আসেন।
কুষাণযুগের পর শুরু হয় গুপ্তযুগ। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কাছে এই যুগটা প্রাচীনকালের হিন্দু-সভ্যতার চরমাবস্থা। এই সভ্যতার ইতিহাস পাঠ করলেই জানা যায়, ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রাধান্যকালে পতিতদের অবস্থা কেমন ছিল। বৌদ্ধ পরিব্রাজকরা এই সময়েই ভারতে এসেছিলেন। তাঁদের রচিত গ্রন্থ থেকে জানা যায় শূদ্র, চণ্ডাল তথা পতিতদের দুরবস্থার ইতিহাস। জানা যায়, নিম্নজাতির মানুষরা এই সময়েই জাতিচ্যুত বলে বিবেচিত হত এবং তাঁদের নগরের বাইরে বসবাস করতে হত। অনেকের মতে, গুপ্ত সাম্রাজ্যেই বর্তমানের ব্রাহ্মণ্যবাদীয় হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ বিবর্তিত শুরু করে। এই সময় থেকেই পৌরাণিক ধর্ম আরও আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে এবং পুরাণসমূহ ও মহাকাব্যগুলি বর্তমান কলেবর প্রাপ্ত হয়েছে। সংকলনের কাজও শেষ হয়। এরপর ভারতে জাতীয়বাদীয় যুগ আরম্ভ হয় এই একজাতীয়তা ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবাধীন হয়। গুপ্ত শাসনকালেই ব্রাহ্মণরা নিজেদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করে ‘ভূ-দেবতা’ রূপে জাহির করতে থাকে। এই যুগে স্মৃতিকারদের মধ্যে নারদ ও বৃহস্পতি ছিলেন প্রধান। এই সময়েই নারদ ‘বিষ্ণুসংহিতা’ গ্রন্থে ব্রাহ্মণদের অবধ্য ও শারীরিক শাস্তিভোগের অতীত বলেছেন। গুপ্তযুগেই পুরোহিত শ্রেণি ভগবানের প্রতিনিধি হয়ে গেলেন। সেই কারণেই তাঁদের সাত খুন মাফ। সেইসঙ্গে রাজারাও যে ভগবানের প্রতিনিধি ও দৈবশক্তিসম্পন্ন, সেটাও প্রচার হতে থাকল। সেটা নথি হিসাবে মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে সংযোজিত হয়। বিষ্ণুসংহিতাতে বলা হয়েছে, “নিম্নশ্রেণির মানুষ উচ্চশ্রেণির মানুষের আসনে বসলে সেই নিম্নশ্রেণির নিতম্বে আগুনের ছাপ দিয়ে নির্বাসিত করে দেবে।” শূদ্রদের উদ্দেশ্যে আরও বলা হয়েছে –“সে যদি থুতু ফেলে তাঁর ঠোঁট কেটে দেবে।” বলা হয়েছে– “শূদ্র জাতিচ্যুত, তাই কোনো জাতিচ্যুত ব্যক্তি সাক্ষীরূপে গৃহীত হবে না।” শূদ্রদের সঙ্গে দ্বিজদের বিবাহ নিষিদ্ধ করে বলা হয়েছে– “দ্বিজেরা যদি নিম্নশ্রেণির স্ত্রীলোককে বিবাহ করে তাহলে তাঁরা তাঁদের পুত্রদের ও বংশকে শূদ্রের স্তরে নামিয়ে দেয়। আর এসব ধর্মোপসনার জন্য রক্তের পবিত্রতা রক্ষার তাগিদেই এমন কঠোর ব্যবস্থা। এই অজুহাতেই নীচজাতির সঙ্গে বিবাহ আহারাদি বন্ধ করা হয়। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক ডা. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্পষ্ট করে বলেছেন –“প্রকৃতপক্ষে ইহা কিন্তু নিম্নশ্রেণি হইতে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপালন করিবার জন্য আলাদা হইবার ফন্দি মাত্র। এই যুগে রাজা ও পুরোহিত উভয়েই ভগবানের সনদপ্রাপ্ত লোক হয়। এই সময়েই গণ-সাধারণকে শোষণ ও লুণ্ঠনের জন্য ধর্ম ও রাষ্ট্র এক হয়।”
কিন্তু খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে গুপ্ত সাম্রাজ্যেও তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে হুন আক্রমণে। হুনরা ছিল মধ্য এশিয়া থেকে আসা এক নিষ্ঠুর ও বর্বর জাতি। হুনদের বাধা দিতে গিয়ে গুপ্তরাজগণ হীনবল হয়ে পড়ে। এখন প্রশ্ন হল– এইসব শক, কুষাণ, হুন, পারদ, গুর্জরদের মতো বিদেশি বর্বর জাতিগুলো ভারতে প্রবেশ করেছিল এবং তাঁরা উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজত্ব করেছিল, তাহলে এঁরা গেল কোথায়? তাঁরা সমূলে নির্বংশ হয়ে গেছে এমন কোনো তথ্য তো পাওয়া যায় না। অতএব অনুমান করে নিতেই পারি, এঁরা কোনো না-কোনো ভারতীয় ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করে স্বকীয়তা খুঁইয়েছে। গ্রিকদের অনেকেই ভারতীয় ধর্ম গ্রহণ করেছিল। এঁদের সকলেরই সত্তা ভারতীয় সমাজে বিলীন হয়ে গেছে। তাঁরা কেউ বৌদ্ধ, কেউ জৈন, কেউবা ব্রাহ্মণ্যবাদীয় হয়ে তথাকথিত হিন্দুধর্মে মিশে যায়। ব্যতিক্রম কেবল বিদেশি আক্রমণকারী মুসলিমরা। মুসলিম আক্রমণকারীরা ভারতে প্রবেশ করেছে, রাজত্ব করেছে দীর্ঘ ৮০০ বছর। কিন্তু তাঁরা কেউই নিজের ধর্মীয় স্বকীয়তা ত্যাগ করে ভারতীয় কোনো ধর্মের ধারেকাছে ঘেঁষেনি। উপরন্তু তথাকথিত হিন্দুধর্মে দারুণভাবে প্রভাব ফেলেছে ইসলাম ধর্ম প্রচুর অমুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ ইসলাম ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে পড়তে থাকল নানা কারণে। ইসলামের এই আগ্রাসন থেকে হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈন-শিখ সকল ভারতীয় ধর্মই ব্যর্থ হল। ইসলাম শাসনকালে সবচেয়ে বেশি ধর্মান্তরিত হয়েছিল তথাকথিত নিম্নবর্গীয়রা। কিন্তু একজন মুসলিমও হিন্দু বা বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে, এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায় না।
সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকেই ভারতীয় হিন্দু-বৌদ্ধ শাসকরা ক্ষমতাচ্যুত হতে শুরু করে। সেই মুসলিম শাসক দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত হিন্দু-বৌদ্ধ রাজাদের বিস্তারিত ইতিহাস তেমন পাওয়া যায় না। সেই পতনের ইতিহাস কেউ বোধহয় লেখার প্রয়োজন বোধ করেনি। তবে মুসলিম শাসনে অমুসলিম শাসকরা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে পড়লেও ব্রাহ্মণ্যবাদীরা নিজেদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ভেদ-বিভাজন কঠোর থেকে কঠোরতর করে চলছিল। সপ্তম থেকে নবম শতাব্দীতে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় মনোবৃত্তি পর্যবেক্ষণ করে সেই সমাজের অবস্থা বোঝা যায়। এ সময়েই রচিত হয়েছিল বেশকিছু কঠোর অনুশাসনযুক্ত গ্রন্থ। তার মধ্যে সৎত্রিমিসাংমাতা’ গ্রন্থে বলা হল –“বৌদ্ধ, পাশুপত্য, জৈন, নাস্তিক কপিলে শিষ্যদের গাত্র স্পর্শ করলে স্নান করতে হয়। পাঠক লক্ষ করুন, মুসলিমরা কিন্তু এই তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে অচ্ছুৎ হয়নি। অচ্ছুৎ সেদিন থেকেই হল যেদিন থেকে নিম্নবর্গীয়রা মুসলিম হতে শুরু করে দিল। নতুন কিছু নয় এটা। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ঠিক যেভাবে হিন্দু নিম্নবর্গীয়দের ঘৃণ্য ও অচ্ছুৎ ভাবত, ঠিক সেই সূত্রেই মুসলিম হয়ে যাওয়া নিম্নবর্গীয়দের ঘৃণ্য ও অচ্ছুৎ করল। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তথাপি নিম্নবর্গীয়দের যথাযথ সম্মান জানিয়ে ফিরিয়ে আনার ন্যূনতম চেষ্টা করেনি। সেদিন যদি ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ব্রাহ্মণ্যবাদে কিঞ্চিৎ শিথিলতা এনে নিম্নবর্গীয়দের যথাযযাগ্য সম্মান জানাতে পারত, তাহলে কখনোই এত সংখ্যক হিন্দু সম্প্রদায় থেকে মানুষ ইসলাম ও বৌদ্ধধর্মে কনভার্ট হয়ে যেত না।
বিদেশি শত্রুদের সঙ্গে বিরুদ্ধে লড়াই করতে হলে প্রথমেই প্রয়োজন ছিল নিজেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা। ঐক্য তো দূরের কথা, উল্টে একটা জাতি ভেঙে হাজার টুকরো হয়ে গেল। ফলে বিদেশি আক্রমণকারীরা পেয়ে গেল ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী একটা গোষ্ঠীর সাহচর্য। তা না-হলে বিদেশ থেকে আসা ভিন্ন ধর্মের একটা জাতি দীর্ঘ ৮০০ বছর ভারত শাসন করতে পারত না। আরও কিছু তথ্য শোনাই আপনাদের। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ‘বিষ্ণুধর্মশাস্ত্র গ্রন্থ লিখে ফেললেন এসময়। কী বলছেন এ গ্রন্থে? বলছেন –“হরিদ্রাবণের বস্ত্র পরিহিত সাধুদের (বৌদ্ধ) ও কাপালিকদের দর্শন মঙ্গলজনক নয়।” এই গ্রন্থে ম্লেচ্ছ, অন্ত্যজদের সঙ্গে বাক্যালাপ পর্যন্ত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ম্লেচ্ছদেশে (সমুদ্র অতিক্রম করে যে দেশে যেতে হয়, কালাপানি) পর্যটনও নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বস্তুত এ সময়ে ব্রাহ্মণ্যবাদী তথা উচ্চবর্গীয় হিন্দুসমাজ নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে উঠেপড়ে লেগেছিল। ফলে হিন্দুসমাজ সংকীর্ণ হতে হতে ক্রমশ কূর্মাবস্থা প্রাপ্ত হতে শুরু করল। মনু, যাজ্ঞবল্ক্যরা বৌদ্ধ দেশগুলিকে ব্রাহ্মণবর্জিত ‘ম্লেচ্ছদেশ’ বলে ঘোষণা করে দিল। অচ্ছুৎ হিসাবে বৌদ্ধ আর মুসলিমদের এক কাতারে দাঁড় করিয়ে দিল বলা যায়। এমনভাবে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণবাদীরা নিজেদের চারদিকে একটা অদৃশ্য পাঁচিল তুলে দিল। এ সময় থেকেই জাতিভেদ, স্পর্শদোষ, বিধর্মীদের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন গেড়ে বসতে থাকল। এমতাবস্থায় শূদ্র-অন্ত্যজ তথা পতিতদের ভাগ্যে অতীব দুর্দশা চিরস্থায়ীভাবে পোক্ত হয়ে গেল। ব্রাহ্মণ্যবাদী ঘূত্মার্গীয় জাতিভেদের ভীষণ কঠোরতা ও বিধিনিষেধ সংবলিত বর্তমান এই ভারতের হিন্দুসমাজের এই সময় থেকেই পাকাপাকিভাবে শুরু গেল, যা আজও প্রবাহমান। ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চবর্গীয়দের উৎপীড়ন সংখ্যালঘু স্বদেশি বৌদ্ধদের দেশ থেকে উৎখাত করতে সক্ষম হলেও সংখ্যালঘু বিদেশি মুসলিম শাসকদের উৎখাত করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। যে জাতি নিজেদের মধ্যে কোন্দল হানাহানি রক্তারক্তি করে থাকে, সেই জাতির দিগ্বিজয় অনেক দূরের স্বপ্ন, জয়ী হতেই পারে না।
পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষক প্রমোদবরণ বিশ্বাস তাঁর ‘ব্রাহ্মণ্যবাদ ও দলিত সমাজ’ গ্রন্থে লিখেছেন– “…বিবেকানন্দ কিন্তু এই দরিদ্র মূর্খদের জন্য কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরি করে যাননি। বরং বাস্তবে তিনি ঠিক এর বিপরীত কাজটিই করে গেছেন। বিবেকানন্দের নিজের হাতে প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন দ্বারা পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে কোন্ সমাজের ছাত্ররা ভর্তি হতে পারবে। তার একটা সুনির্দিষ্ট ধারা তিনি রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সংবিধানে নিজের হাতে Fotelcata– Only the Hindu boys of good family will be admitted in this mission.’ অর্থাৎ একমাত্র কুলীন হিন্দু পরিবারের ছেলেরাই এই মিশনে ভর্তি পারবে। এই গোপন সার্কুলারের মধ্য দিয়েই আমরা প্রকৃত বিবেকানন্দকে দেখতে পেলাম। সুতরাং দলিতদের দৃষ্টিতে স্বামী বিবেকানন্দ আসলে হঠকারী ব্যক্তিত্ব। তাই তো দেখি রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দরিদ্র, মূর্খ, চাষাভূষো তফসিলি এবং আদিবাসী সমাজের ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির জন্য সংবিধান নির্দেশিত সামান্য সংরক্ষণ প্রথাও মান্য করা হয় না। আর সংরক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ তো দূর অস্ত! কারণ এতে নাকি মিশনের ঐতিহ্য নষ্ট হয়ে যাবে।”
“স্বধর্মে নিধনং শ্ৰেয় পরধর্মো ভয়াবহঃ”– এই শ্লোকটি গীতায় পাওয়া যায়। এখানে যে ধর্মের কথা বলা হয়েছে, সেটা হিন্দুধর্ম নয়। সেই ধর্ম ব্রাহ্মণদের ধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্ম। এ সময় দুটোই ধর্ম– একটি আর্য ধর্ম, অন্যটি অনার্য ধর্ম। আবার চতুর্বর্ণের মধ্যে একে অপরের বিচারে ‘পরধর্ম’। বর্ণবাদী ব্রাহ্মণেরা শ্রীকৃষ্ণের মুখে কথাগুলি বসিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করেছেন। সে সময় বর্তমান হিন্দুধর্মের মতো সন্মিলিত ধর্মের সৃষ্টি হয়নি, সে সময়ের ভারতীয় ধর্মকে সনাতন ধর্ম বললেই সঠিক হয়। গীতায় উল্লিখিত এই ধর্ম আসলে ব্রাহ্মণ ধর্ম, ক্ষত্রিয় ধর্ম, বৈশ্য ধর্ম এবং শূদ্র ধর্ম। এই ধর্ম রক্ষা করতেই ত্রেতাযুগের রাজা রামচন্দ্র শূদ্র শম্বুককে হত্যা করেছিলেন। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি তপস্যা করে ব্রাহ্মণ হতে চেয়েছিলেন। তার অপরাধ, তিনি লুকিয়ে বেদ পাঠ করেছিলেন। ঘটনাটি এ রকম : এক কুলিন ব্রাহ্মণের বালকপুত্র অসময়ে মারা যায়। রাজপুরোহিতরা রামকে বলেন, “রাজ্যে কেউ পাপ করেছে, যার ফলে এই অঘটন ঘটছে”। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, শম্বুক নামে এক শূদ্র সশরীরে দেবত্ব পাওয়ার জন্যে তপস্যা করছে এবং তা সে নিজেই সেই কথা স্বীকার করল (রামায়ণ : ৭/৬/২)। “সেই শূদ্রটি কথা বলতে বলতেই উজ্জ্বল খঙ্গ কোশ থেকে বের করে তার শিরোচ্ছেদ করলেন রাঘব।” তখন দেবতারা রামকে সাধুবাদ দিয়ে বললেন, “রাম তুমি দেবতাদের কার্যসাধন করলে, তোমার জন্য এই শূদ্র স্বভাক হতে পারল না।” (পৃ: ১৩)
রাবণ, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ, শূর্পণখা হত্যা তো আসলে শূদ্র তথা অনার্য হত্যাই। শূদ্র নির্যাতনের আর-একটি কাহিনি সকলেই কিছুটা জানেন, যা মহাভারতে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি এরকম : একলব্য ছিলেন মগধের অধিবাসী নিষাধরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র। গুরুদেব দ্রোণের কাছে একলব্য গিয়েছিলেন যুদ্ধবিদ্যা শিখতে। কিন্তু একলব্য ক্ষত্রিয় ছিল না বলে দ্রোণ তাকে শিষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি হননি। কিন্তু বালক একলব্য দ্রোণকেই গুরু মেনে গহীন বনে একমনে যুদ্ধবিদ্যা শিখতে থাকে। একদিন দেখা যায় একলব্য দ্রোণের ক্ষত্রিয় শিষ্যদের চেয়েও বড়ো যোদ্ধা হয়ে গেছেন। বনে ঘুরতে এসে একদিন দ্রোণ একলব্যের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে জানতে চান কে তার গুরু। একলব্য দ্রোণকেই গুরু বলে জানায়। দ্রোণ তখন পশ্চিমাকাশে কালো মেঘ দেখতে পান। দূরদর্শী দ্রোণ গুরুদক্ষিণা হিসাবে একলব্যের ডানহাতের বুড়ো আঙ্গুল দাবি করে বসলেন। ডানহাতের বুড়ো আঙ্গুল কেটে ফেলা মানে ধনুক চালানো সারাজীবনের জন্য শেষ। তা সত্ত্বেও সরলমনা একলব্যকে বিনাবাক্যে গুরুকে তা দিয়ে দিতে হল। আঙ্গুল কেটে দিতেই হত। না-হলে তাঁকে নিশ্চিত মৃত্যুবরণ করতে হত। দ্রোণাচার্য নিশ্চয় তাঁকে ক্ষমা করতেন না। এই ঘটনাটিকে অনেকে অত্যন্ত মহান হিসাবে দেখে থাকে। কিন্তু আমি সেভাবে দেখতে পারছি না। খুঁজে দেখা যাক কেন একলব্যকে তাঁর অত্যন্ত মূল্যবান বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি খোয়াতে হল। কারণ— (১) শিক্ষাগুরুর প্রত্যক্ষ উপস্থিতি ছাড়াই একলব্য যে অস্ত্রবিদ্যা অর্জন করেছিল, সেই বিদ্যা তখনও পর্যন্ত দ্রোণের খাসশিষ্য অর্জুনের পক্ষে শেখা হয়ে ওঠেনি। কেন-না ব্রাক্ষণ ও ক্ষত্রিয় তথা দ্বিজ ছাড়া অন্য কারোকেই শিক্ষালাভ ও শিক্ষাদানের অধিকার দেওয়া হয়নি। কেবলমাত্র ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা উপযুক্ত দক্ষিণার বিনিময়ে নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে শিক্ষালাভ করতে পারত। শূদ্রের বেলায় যে-কোনো শিক্ষাই নৈব নৈব চ।
অপস্তম্ভ ধর্মসূত্রে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে– শূদ্র যদি বেদ পাঠ করে তবে তাঁর জিহ্বা কর্তন করা হবে এবং যদি বেদপাঠ শ্রবণ করে তাঁর কর্ণে গরম সিসা ঢেলে দেওয়া হবে। অতএব ক্ষত্রিয় অর্জুনকে পিছনে ফেলে শূদ্র একলব্য সামনে এগিয়ে যাবে, তা কী করে হয়! মাহাত্ম দিয়ে কী মল ঢাকা যায়? কারণ –(২) একলব্য ছিলেন মগধ দেশের উপজাতি। এই মগধের রাজা ছিলেন জরাসন্ধ এবং সেনাপতি ছিলেন শিশুপাল। মগধ ছিল হস্তিনাপুরের শত্রুদেশ, তাই হস্তিনাপুরের অন্নজলে প্রতিপালিত দ্রোণাচার্য চাননি যে, তাঁর বিদ্যা হস্তিনাপুরের বিপক্ষে প্রয়োগ হোক। একলব্য অজেয় হয়ে উঠলে দ্রোণের সমূহ বিপদ। দ্রোণের মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে না। কী সেই মনোবাঞ্ছ? দ্রোণের সঙ্গে দ্রুপদরাজার ভয়ানক শত্রুতা ছিল। দ্রুপদরাজাকে উচিত শিক্ষা দিতে অর্জুনকেই দ্রোণের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল। দ্রোণ কৌরব-পাণ্ডবদের অস্ত্র শিক্ষা শেষে গুরুদক্ষিণা হিসাবে দ্রুপদকে বন্দি করে আনার কথা বললে, এঁরা দ্রুপদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং অর্জুন দ্রুপদকে বন্দি করে দ্রোণের কাছে নিয়ে আসেন। দ্রুপদের মৃত্যু হয় দ্রোণের শাণিত অস্ত্রেই এবং দ্রুপদ রাজার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের খড়গ দ্বারা দ্রোণের শিরচ্ছেদ হয়।
যদিও রামায়ণ-মহাভারত মহাকাব্য বই অন্য কিছু নয়, তা সত্ত্বেও বলব এই মহাকাব্য দুটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। এই মহাকাব্য দুটিতে প্রচুর ইতিহাসের উপাদান আছে, যা তৎকালীন সমাজব্যবস্থার ছবি রক্ষিত আছে। সেই সমাজব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের প্রতাপ ছিল দোর্দণ্ড। এঁদের নির্দেশ ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়তে সাহস পেত না। রামায়ণ মহাভারতের পরতে পরতে মনুসংহিতার নির্দেশিত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-শূদ্রের ছবি স্পষ্ট হয়েছে। সেইজন্য বোধহয় ব্রাহ্মণ্যবাদের কর্তৃত্বে এই মহাকাব্য দুটি ধর্মীয় গ্রন্থের সম্মান পায়। মহাভারতে আমরা দেখতে পাই ক্ষত্রিয় সমাজের অস্ত্রশিক্ষাও ব্রাহ্মণগণ নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছেন। ক্ষত্রিয় নন, অথচ পরশুরাম, দ্রোণাচার্য প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ অস্ত্রগুরু হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। রাজকার্য পরিচালনাতেও তাঁরা ক্ষত্রিয়দের অভিভাবক হন। ব্রাহ্মণসেবা ও তাঁদের নির্দেশ পালন করাই হল ক্ষত্রিয় রাজার অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। তাই ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠের নির্দেশে ক্ষত্রিয় রামচন্দ্র শূদ্ৰপণ্ডিত শম্বুকের ধড় থেকে মুণ্ডু আলাদা করে দেন। সেই সময়কার সমাজে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়রা কতটা ‘পাওয়ারফুল’ ছিলেন, তার বিস্তারিত বর্ণনা আমি আমার ‘যুক্তিবাদীর চোখে রাম ও রামায়ণ’ গ্রন্থে আলোচনা করেছি।
ভগবান (?) মনু যতভাবেই প্রত্যাখ্যাত হোন-না-কেন, বৃহত্তর সংখ্যার মানুষ কিন্তু মনুর প্রভাব থেকে কোনোভাবেই মুক্ত হতে পারছেন না। আজও নানাভাবে সমাজে এবং বর্তমানের আধুনিক সমাজে আবর্তিত হচ্ছেন। মনু তাঁর হিন্দুত্বের প্রলম্বিত ছায়া দিয়ে আধুনিক সময়ের সমাজকে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রাখার চেষ্টা করে চলেছেন। সেই চেষ্টা উচ্চবর্ণেরা তো করেই, তার চেয়ে বেশি করে নিন্মবর্ণেরা। এমনকি দেখা যায়, উচ্চবর্ণদের কেউ কেউ যদিও উদারতার পরিচয় দিতে চায়, সেক্ষেত্রে নিন্মবর্ণের মানুষেরাও নিদান নিয়ে আসে, হিন্দুধর্ম শেখায়। মনুবাদে এত আনুগত্য! যদিও ২০০০ সালের ৩০ জানুয়ারি ‘পাইওনিয়ার’ পত্রিকায় তথ্য দিয়ে ছাপা হয়েছিল– জাতপাত ব্যবস্থাভিত্তিক ধর্মের অনুশাসনে ভারতে শত শত বছরে লক্ষ লক্ষ দলিত নিহত হয়েছেন শুধুমাত্র দলিত হওয়ার অপরাধে। তার মধ্যে প্রায় ত্রিশ লক্ষ দলিত নিহত হয়েছে স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে। জ্ঞাতসারেই হোক কিংবা অজ্ঞাতসারে –মনুর নির্দেশ নিরন্তর পালিত হয় সারা ভারতেই।
মনু শূদ্র নিধনের জন্যে তো প্রেরণা দিয়েই রেখেছেন তাঁর মূল্যবান সংহিতায়। একাদশ অধ্যায়ের ১৩১ নম্বর শ্লোক তথা নির্দেশে বলছেন –একটা শূদ্র হত্যা করলে একটা বিড়াল বা নকুল বা চাষপক্ষী বা ভেক বা কুকুর বা গাধা বা পেচক বা একটা কাক পাখি হত্যার সমান পাপ হয় এবং সেই পাপ স্খলনের জন্যে ঠিক ততটুকুই প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।
“মার্জারনকুলৌ হত্বা চাষং মণ্ডুকমেব চ।
শ্বগোধোককাকাংশ্চ শূদ্ৰহত্যাব্রতং চরেৎ।”
একজন শূদ্ৰহত্যা একটি ব্যাঙ হত্যার সমান। খুবই ক্ষুদ্র বা তুচ্ছ কাজ বটে! উচ্চবর্ণের হিন্দুত্ববাদীদের মদতে পুষ্ট বিহারের রণবীর সেনা’ নামের সংগঠন শূদ্ৰহত্যার কাজে নিবেদিতপ্রাণ। ভারতে প্রতি ঘণ্টায় দুজন শূদ্র প্রহৃত হয়, প্রতিদিন ধর্ষিতা হন তিনজন দলিত নারী, প্রতিদিন খুন হচ্ছেন দুজন দলিত এবং পুড়িয়ে দেওয়া হয় দুটি দলিত-গৃহ (Report of the Ministry of Welfare of the Government of India, 1992-1993),
এহেন ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং ব্রাহ্মণদের গা-জোয়ারি ফতোয়া যে সকলে মুখ বুজে মেনে নিয়েছেন, তা কিন্তু মোটেই নয়। প্রতিবাদ যেমন হয়েছে, বিদ্রোহও হয়েছে। প্রতিবাদ যে হয়েছে তার প্রমাণ চার্বাক, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম বা দর্শন ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ফল। এইসব ধর্ম বা দর্শন গড়ে উঠেছিল ব্রাহ্মণ্যবাদের সৃষ্ট অস্পৃশ্যতা ও পতিতদের ঘৃণার বিরুদ্ধেই। এইসব ধর্ম বা দর্শন সমাজের প্রান্তিক অচ্ছুৎ ব্রাত্য দলিত শূদ্র পতিত অন্ত্যজদের সাম্যবাদের সমাজ উপহার দিল। বিরোধিতা বা মুখ খোলার পরিণাম কী হয়েছিল তা ইতিহাসেই রক্তের অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে।
সম্ভবত চার্বাকরাই সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন। শুধু ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধেই নয়, প্রতিবাদ করেছে বেদের বিরুদ্ধেও। তাই চার্বাকরা নাস্তিক তকমা পেল এবং নিশ্চিহ্ন হতে হল। পারলৌকিক নয়, ইহজাগতিক সুখ ভোগই মানুষের একমাত্র কাম্য’ বলে চার্বাকরা মনে করত। চার্বাক দর্শনের প্রভাব বুদ্ধের সময় ও প্রাক-বুদ্ধ যুগে উপস্থিত ছিল বলে অনেকে মনে করে থাকেন। মৈত্ৰায়ণীয় ও ছান্দোগ্য উপনিষদের রচনাকালেই চার্বাক মতবাদের গোড়াপত্তন হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। ঐতরেয় উপনিষদের কিছু অনুচ্ছেদে দেহাত্মবাদ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদে মরণোত্তর চৈতন্যের অস্তিত্বের অস্বীকৃতির স্বপক্ষে কিছু শ্লোকের উল্লেখ পাওয়া যায়। কঠ উপনিষদের পরলোকগামী আত্মার অস্তিত্বে অবিশ্বাসী সম্প্রদায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদ ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ববর্তী বলে অনুমান করা হলে চার্বাক মতের জন্ম এই কালেই হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায়।
চার্বাকগণের মতাদর্শ অনুসারে, ব্রাহ্মণরা হিন্দু নয়। বেদ, গীতা, মনুসংহিতা ইত্যাদি ব্রাহ্মণ্যধর্মের শাস্ত্র। চতুর্বর্ণপ্রথা, জাতপাত, অস্পৃশ্যতা এগুলি ব্রাহ্মণ্যধর্মের জিনিস। ব্রাহ্মণ্যধর্ম হিন্দুধর্ম নয় বা হিন্দুধর্মের কোনো অংশ নয়। ব্রাহ্মণ্যধর্ম হিন্দুধর্মের উপর পরগাছার মতো চেপে বসা একটি ধর্ম। আর এই ব্রাহ্মণ্যধর্মকে অবলম্বন করেই ব্রাহ্মণরা হিন্দু জাতির উপর আধিপত্য করে যাচ্ছে। হিন্দু জাতির উপর ব্রাহ্মণদের আধিপত্য কায়েম করার জন্যই ব্রাহ্মণ্যধর্মের সৃষ্টি। ব্রাহ্মণ্যধর্মকে সেভাবেই তৈরি করা হয়েছে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিধিবিধান, নিয়মনীতি, সত্যাসত্য বোধ বা পাপপুণ্যের ধারণাকে সেভাবেই সাজানো হয়েছে, যাতে তা নিঃসংশয়ে হিন্দুজাতির উপর ব্রাহ্মণদের প্রভুত্বকে কায়েম করে এবং হিন্দু জাতিকে ব্রাহ্মণদের বিশ্বস্ত ও অনুগত ক্রীতদাসে পরিণত করে।
এইভাবেই চার্বাকগণ ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরোধিতা করতেন। কিন্তু লোকবল, বাহুবল এবং অস্ত্রবল না-থাকায় ব্রাহ্মণ্যবাদীদের রক্তচক্ষুর সামনে চার্বাকগণ পরাস্ত এবং নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল চিরতরে।পুড়িয়ে দেওয়া হল চার্বাকদের রচিত গ্রন্থসমূহ। যদি চার্বাকরাও সশস্ত্র প্রতিপক্ষ হিসাবে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সঙ্গে সঙ্গে সমানে সমানে টক্কর দিতে পারত, তবে হয়তো অন্য এক ভারত দেখতে পেতাম। মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধরা এভাবে লাখো লাখো হিন্দুদের ধর্মান্তরে নিয়ে যেতে পারত না। এত সাম্প্রদায়িক হানাহানি হত না।
ব্রাহ্মণবাদীরা চার্বাকদের নিশ্চিহ্ন করতে এক তুড়িতে সমর্থ হলেও, বৌদ্ধদের সঙ্গে তেমন এঁটে উঠতে পারেনি। ব্রাহ্মণ্যবাদের চরম বিরোধিতা করে বৌদ্ধদর্শন এবং বৌদ্ধ অনুগামীরা সারা ভারতে অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকল। প্রাক-বুদ্ধ ও বুদ্ধ-পরবর্তী সমাজে ব্যাপক ক্রীতদাস প্রথা ছিল, ভয়ংকর দারিদ্র্য ছিল। অত্যন্ত চড়া সুদে ঋণ দিতেন শ্ৰেষ্ঠী, বণিক, ধনী সম্প্রদায়। ঋণে জামিন হিসেবে সম্পত্তি না রাখতে পারলে বউ, বোন বাঁধা রাখতে হত ঋণদাতার কাছে। এই মহিলাদের শ্রমের সঙ্গে দেহ দিতে হত। এরপর ঋণ শোধ না হলে ঋণগ্রহীতাকে দাস হিসাবে থাকতে হত ঋণদাতার কাছে। দারিদ্র্য ও দাসত্বের এই যন্ত্রণা ও দুঃখছিল ভয়ংকর। শ্রমজীবী শূদ্রদের জীবনও ছিল বিভীষিকাময়। দিন থেকে রাত কঠোর শ্রমের বিনিময়ে একবেলা উচ্ছিষ্ট খাবার মিলত। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলোতে যাঁদের শূদ্র বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, বৌদ্ধগ্রন্থে তারাই চণ্ডাল, নেসাদ, পুকুস নামে পরিচিত। পরিচয় পাল্টালেও ধনী মহাজনদের উৎপীড়ন একই রইল। শোষিত শূদ্ররাও বৌদ্ধধর্মকে গ্রহণ করে ঘৃণ্য জীবন থেকে মুক্তি পেয়েছিল।
উচ্চবর্ণের ভারতীয় দার্শনিক ও ঐতিহাসিকরা বুদ্ধকে উপজাতীয় থেকে ক্ষত্রিয় বানিয়ে ছেড়েছেন। শুদ্ধোধনকে বানালেন রাজা। অথচ বুদ্ধের সময়কার ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের মানুষদের কাছে বুদ্ধ ছিলেন নীচবংশীয় মানুষ। চরক, সুশ্রুত, নাগার্জুন, ভাস্করাচার্য, বাৎসায়ন, কৌটিল্য, পাণিনি, অশ্বঘোষ প্রমুখ মননশীল পণ্ডিতরা ছিলেন বৌদ্ধ বা বৌদ্ধভাবাশ্রয়ী। বৌদ্ধযুগে একটা সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটে গিয়েছিল। ভারতবর্ষে তখন বৌদ্ধধর্ম রয়েছে। বৌদ্ধ ধর্ম হল উদার। জাত পাত-বর্ণ নেই। সবাইকে গ্রহণ করতে হাত বাড়িয়েই আছে। এই অবস্থায় বিদেশ থেকে আগত রাজশক্তি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করাকেই সম্মানজনক মনে করেছিলেন। এই কারণেই গ্রিক, শক, কুষাণ প্রভৃতি রাজশক্তি ও তাঁদের সঙ্গে আসা সৈন্য-সামন্ত বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। ফলে স্বাভাবিক নিয়মেই বৌদ্ধধর্ম রাজশক্তির সহযোগিতায় তুঙ্গে উঠেছিল। বৌদ্ধধর্মের উত্থান ঠেকাতে কিছুটা কৌশল গ্রহণ করল। ব্রাহ্মণবাদীরা গ্রিক, শক, কুষাণদের ‘পতিত ক্ষত্রিয়’ বলে আখ্যা দিল। এতে দুটি ঘটনা ঘটল— (১) ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বর্ণপ্রথা বড়ো ধরনের ধাক্কা খেল। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের একটা বড়ো অংশই বর্ণের নতুন সমীকরণ মেনে নিল না। (২) সমাজের বহু নিচু বর্ণের মানুষ বিদেশিদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে সমাজের দু-এক ধাপ উপরে উঠতে চেষ্টা করল। এরপর একটা প্রশ্ন উঠে আসতেই পারে, সম্রাট অশোক তো বিদেশি ছিলেন না, তিনি কেন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন? যুদ্ধ, গণহত্যা, লুণ্ঠন, রক্তপাতের মধ্য দিয়ে অশোক তাঁর রাজত্বকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করেছিলেন। এই বিস্তৃতির পিছনে নিষ্ঠুর সামরিক শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয়েছে। বস্তুত সেই রক্তাক্ত হাত ধুয়ে ফেলতেই ধর্ম পরিবর্তন করে নিরামিষাশী হয়ে গেলেন। সবাই বললেন। ‘বোধোদয়। তারই পরিণতিতে অশোক অহিংস বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।
বৌদ্ধধর্মের নিরন্তর প্রসারে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ভীত হয়ে পড়লেন। ব্রাহ্মণদের ফতোয়ায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠা শূদ্র তথা অন্ত্যজরা ব্রাহ্মণ্যধর্ম ত্যাগ করে দলে দলে বৌদ্ধধর্মে চলে যাচ্ছিলেন। সংকটে পড়ে গেল ব্রাহ্মণ্যধর্ম। অপ্রতিরোধ্য বৌদ্ধধর্মকে প্রতিরোধ করতে আদি শঙ্করাচার্যকেও আসরে নামতে হয়েছিল। তাঁরা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিল বৌদ্ধধর্মে যাওয়া আর ব্রাহ্মণ্যধর্মে থাকা একই ব্যাপার। কারণ ভগবান বুদ্ধ স্বয়ং বিষ্ণুরই অবতার। বুদ্ধ ব্রাহ্মণ্যধর্মেরই অংশ। বলা হয় বৌদ্ধধর্ম সবসময়ই হিন্দুধর্মের ভিতরেই। বর্তমান ভারতের সংবিধানেও বৌদ্ধ, জৈন, শিখদের হিন্দুধর্ম হিসাবে দেখানো হয়েছে, যা নিয়ে সুপ্রিমকোর্টে মামলা পর্যন্ত। কিন্তু সে বিষয়ে আজও কোনো নিষ্পত্তি হয়নি। যদি এঁরা হিন্দুধর্মের মধ্যেই, তবে বুদ্ধের সংস্কার হিন্দুধর্ম কেন মেনে নেয়নি, তার উত্তর পাওয়া যায় না। যাই হোক, ব্রাহ্মণ্যবাদের তীব্র প্রভাবে বৌদ্ধরা ভারতে গুটিয়ে গেলেও ভারতের বাইরে বিস্তার লাভ করতে কোনো অসুবিধাই হয়নি।
পরবর্তীতে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কাছে খুব চাপ হয়ে গেল ভারতে মুসলিমদের আগমনের পর। রিচার্ড ইটনের প্রামাণিক গ্রন্থ “দি রাইজ অফ ইসলাম অ্যান্ড দি বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ার’ সূত্র থেকে জানা যায়, মোগল যুগে কোন্ অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের নতুন কারণে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলায় কৃষকরা ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এই আকৃষ্ট এতটাই ছিল যে অবিভক্ত বাংলাদেশে মুসলিমরাই সংখ্যাগুরু হয়ে গেল। কীভাবে? সহজিয়া দর্শনের প্রথম সাংস্কৃতিক প্রকাশ ঘটেছিল নবম-দশম শতাব্দীতে বাংলা ভাষার আদি স্রষ্টা সিদ্ধাচার্যের রচিত চর্যাপদে। চর্যাপদে যে সহজ’ সাধনার প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়েছিল তা ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রাতিষ্ঠানিকতার সব শৃঙ্খল পরিত্যাগ করতে উন্মুখ ছিল। সহজিয়া দর্শনে আত্মোপলব্ধির জন্য, বিগ্রহ ও ব্রাহ্মণের প্রয়োজন নেই। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সেনবংশের রাজাদের অপসারিত করে তুর্ক-আফগান সেনানায়করা সংগঠিত সেনাবাহিনী নিয়ে বাংলার সমাজে নতুন প্রক্রিয়ার উদ্ভবের সূচনা করে। বলাই বাহুল্য, তুর্ক-আফগান সেনানায়কদের ধর্ম ছিল ইসলাম। সে সময় ব্রাহ্মণ্যধর্মের জাতপাতের জাঁতকলের নিষ্পেষণ থেকে মুক্তি পেতে নিম্নবর্গের মানুষেরা ইসলাম ধর্মে চলে আসে। জোর করে ভয় দেখিয়ে মুসলমানরা ব্রাহ্মণ ধর্মাবলম্বীদের ইসলাম ধর্মে টেনে আনা হয়েছিল, একথা সর্বৈ সত্য নয়। যে ইসলামকে বাঙালি মুসলমান গ্রহণ করেছিল তা গোঁড়া মোল্লা ও মৌলভীদের ধর্মীয় আদেশ দ্বারা পরিচালিত হয়নি। সেই গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ইসলামের সুফি মতবাদের প্রভাব সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়েছিল। কারণ তার মেলবন্ধন ঘটেছিল প্রাক-মুসলিম সহজিয়া’ মানবধর্মের সঙ্গে, বিশেষত সমন্বয়ধর্মী ‘নির্গুণ’ বাউল সহজিয়াদের সঙ্গে লোকায়ত স্তরে। সুফি সাধকরা বাংলার সহজিয়াদের কাছে এসেছিলেন, কারণ উভয়ই বাংলার সমাজে ব্রাহ্মণ্যধর্মের আরোপিত বর্ণভেদের বিরোধিতা করতে প্রস্তুত ছিলেন। উভয়ই গোঁড়া হিন্দু পণ্ডিত ও মুসলমান শাস্ত্রজ্ঞদের অসহিষ্ণুতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন। সুফি দর্শনের মেলবন্ধনের প্রক্রিয়াটি সক্রিয় ছিল বাংলার তুর্ক আফগান ও মোগল রাজত্বকালেসেই মেলবন্ধনের প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপটেই নিম্নবর্গের মানুষরা ইসলামকে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল, সক্ষম হয়েছিল লোকায়ত সমন্বয়বাদী দর্শনের আধারে। ইসলাম ধর্মকে কখনো জোরপূর্বক চাপানো হয়নি তুর্ক-আফগান ও মোগল রাজত্বের সময়। এই ধর্মের প্রসার ঘটেছিল সুফি সাধকদের সমন্বয়বাদী তৎপরতার ফলে।
১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে জনগণনা হয়। এই সময় থেকে বাঙালি জাতির উদ্ভব বিকাশ ইত্যাদি নিয়ে কথা শুরু হয়। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দেই জনগণনা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় স্থানীয় মুসলমানরা বেশিরভাগই তথাকথিত নিচুজাতের হিন্দুসমাজ থেকে উদ্ভূত। ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে সারা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ইসলাম ধর্মের প্রচার শুরু হয়। তখনকার সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিরাট অংশের নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলাম ধর্মে চলে আসে।
নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলাম ধর্মে গেলেন কেন? শুধুই কি জাতপাতের ঘৃণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, নাকি অন্য কোনো কারণ? ইসলাম ধর্মের তত্ত্বে কি জাতিভেদের কোনো স্থান নেই? জাতপাত ইসলাম ধর্মেও আছে। সমগ্র ইসলামি সমাজকে প্রধানত দু-ভাগে ভাগ করা যায় –(১) শিয়া এবং (২) সুন্নি। শিয়াকে আবার দুই ভাগে ভাগ হয়েছে– (১) ইসনে আসারিয়া এবং (২) ইসমাইলিয়া। অপরদিকে সুন্নিদেরও দুই ভাগে ভাগ করা হয়– (১) শরিয়তি এবং (২) মারফতি। শরিয়তিও দুই ভাগে বিভক্ত– (১) হানাফি এবং (২) মোহম্মদী/আহলে হাদিস। হানিফরা চারভাগে বিভক্ত –(১) হানাফি, (২) সাফি, (৩) হাম্বলি ও (৪) মালেকি। এইভাবে ৮০টি ভাগ জানা যায়।
দারিদ্র্য আর বর্ণবৈষম্যের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পেতে এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার আশায় বৌদ্ধধর্ম, খ্রিস্টধর্ম কিংবা ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়ে পড়েন লক্ষ লক্ষ দলিত। ধর্মের পরিবর্তন হয়েছিল বটে, তবে ভাগ্যের পরিবর্তন হয়নি। এমনই একজন ধর্মান্তরিত মুসলিম মাহবুব তালুকদার। পেশায় ধোপ মাহবুব সামাজিক গ্রহণযোগ্যতার আশায় ধর্মান্তরিত হন। পূর্বনাম দীপক থেকে মাহবুব হয়ে যায়। অল্পদিনের মধ্যেই সে বুঝে যায় ধর্মান্তর কোনো সমাধান নয়। তিনি জানান ‘ধর্মান্তরিত হওয়াটা কোনো সহজ ব্যাপার নয়, তাঁরা বলে এটা ঠিক নয়। আমি জিজ্ঞাসা করি, কেন? তাঁরা জানায় এর কারণ ভারতে মুসলিমদের খুব সুনাম নেই। চলে হত্যার চেষ্টা। আর-এক দলিত মইনুল ইসলামকে তো ধর্মান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্রে রীতিমতো জীবন বাজি পর্যন্ত রাখতে হয়েছিল। ধর্মান্তরের পূর্বনাম সমীর বাগদি। তিনি জানান, ধর্মান্তরের চেষ্টায় তাঁকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল। মইনুল ইসলাম বলেন, ‘যখন একজন মানুষ ধর্মান্তরিত হয়, তখন নতুন ধর্মের লোকেরা তাঁকে স্বাগত জানায়। কিন্তু পুরোনো ধর্মের লোকেরা তাঁকে থামানোর চেষ্টা করে। যদি থামাতে না পারে, তবে তাঁরা তাঁকে হত্যার চেষ্টা করে। সেটাই আমার সঙ্গে হয়েছে। হিন্দুধর্ম থেকে যাঁরা ইসলাম বা খ্রিস্টধর্মে চলে গেলেন তাঁরা আর পুরোনো ধর্মে ফিরে এলেন না কেন? কারণ হিন্দুধর্ম থেকে যাওয়া যায়, কিন্তু ফেরা যায় না। ফেরার কোনো পথ খোলা নেই। কারণ ধর্মান্তর হয়েছ মানেই তুমি ম্লেচ্ছ, অচ্ছুৎ। ফেরতযোগ্য নও।
হিন্দু সমাজে জাতবর্ণ প্রথা এক সচল প্রথা। চতুর্বর্ণের অজস্র উপবিভাগ এবং সংকর জাতগুলির উদ্ভব এক দীর্ঘ সময়ের প্রক্রিয়ার ফসল। বৃত্তি ও তৎসংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যগুলি ধর্মান্তরিত জনগণের মধ্যে বেঁচে থাকায় কসাইরা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছিল। আর প্রাচীন ভারতে যাঁরা যত শ্রম করে তাঁরা তত ঘৃণিত নীচুজাত। বৃত্তি বাহিত হয়ে পুরুষানুক্রমে এই বৈশিষ্ট্য ইসলামি জনগণের মধ্যেও বাহিত হয়েছে। তাই বলে ইসলামে জাতপাত নেই, একথা বলা যায় না। তবে ছোটোজাতের মানুষগুলো কতটা ঘৃণিত হয়ে থাকে তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে।
মুসলিম শাসনের প্রায় ৮০০ বছরে এই ভারত উপমহাদেশে জাতপাত নিয়ে বহু জলঘোলা হয়েছে। জাতপাতের ঘৃণা থেকে মুক্তি পেতে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষগুলো বারবার অবস্থান পরিবর্তন করেছে। ধর্মান্তরিত হয়েছে। গোষ্ঠী বদল করেছে। জাতপাতের ইস্যু নিয়ে মুসলিম শাসন চলাকালীনই উত্থান হয়েছে ব্রাহ্মসমাজ, বৈষ্ণব আন্দোলন, খ্রিস্টান বা মিশনারিদের। ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রাহ্মসভা উনিশ শতকে স্থাপিত এক সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন, যা বাংলার পুনর্জাগরণের পুরোধা হিসাবে পরিচিত। কলকাতায় ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে ২০ আগস্ট হিন্দুধর্ম সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) ও তাঁর বন্ধুবর্গ মিলে এক সার্বজনীন উপাসনার মাধ্যমে ব্রাহ্মসমাজ শুরু করেন। কিন্তু কেন এ ব্রাহ্মসমাজ? বস্তুত ব্রাহ্মসভার মূল বক্তব্য ছিল, ঈশ্বর এক ও অভিন্ন, সকল ধর্মের মূল কথা এক। রাজা রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার দত্তের মতো প্রসিদ্ধ মানুষেরা এই আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন। একেশ্বরবাদ, ধর্মের গোঁড়ামি, শাস্ত্রীয় আচারপালন, কুসংস্কার এবং অবশ্যই জাতিভেদ প্রথা পুরোপুরি বিলোপ করার পক্ষে মত প্রকাশ করেন তাঁরা। ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য হিন্দু সমাজে প্রচলিত বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলিন্য প্রথা, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন প্রভৃতি কুপ্রথার অবসান ঘটানো। সেই সঙ্গে নারীদের মধ্যে উচ্চশিক্ষার প্রচলন করে ভারতীয় নারীদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা। তবে ব্রাহ্ম আন্দোলন। আর বেশি দূর অগ্রসর হতে পারেনি, বরং দিনে দিনে শক্তি হারাতে থাকে। অর্থাৎ ব্রাহ্মসমাজের মানুষরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের তীব্র বিরোধিতা করলেও, ব্রাহ্মণ্যধর্মের দাপটে ব্রাহ্মসমাজ বৃহত্তর মনুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। তাই এই সমাজ সমাজে প্রান্তিক হয়েই রইল।
শ্রীচৈতন্য মধ্যযুগে, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার নবদ্বীপে, আর্যাবর্তেও বৈদিকধর্মের চতুর্বর্ণ প্রথার (Caste System) নিষ্পেষণ এবং বিদেশি শাসকদের নির্যাতনের বিরুদ্ধে এক অহিংস আধ্যাত্মিক আন্দোলনের সঞ্চার করেন, যার নাম গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম। ধর্মগুরু আর রাজ-শাসনের অত্যাচারে জর্জরিত বাংলার দিশেহারা অন্ত্যবর্ণ সাধারণ জনগণকে তিনি মুক্তির পথ দেখিয়েছেন, ঐক্যবদ্ধ করেছেন এবং নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহস জুগিয়েছেন এই আন্দোলনের মাধ্যমে। তাঁর আবির্ভাবে এবং কর্মতৎপরতায় গণমানুষের উদ্যোগে তৎকালীন সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। মানুষ হিসেবে জন্মলাভ করে স্বাভাবিক মনুষ্য জীবনযাপন করা সম্ভব হয়। ধর্মের জন্য মানুষ না-হয়ে মানুষের জন্য ধর্ম— এই বোধ সৃষ্টি হয়। বাংলা ভাষায় বৈষ্ণব সাহিত্যের নতুন ধারা সৃষ্টি হয়, যা গণমানুষকে জাগাতে সাহায্য করে। বাংলার সংস্কৃতিতে উদারনৈতিকতা, সহনশীলতা ও সাহসিকতার রূপান্তর ঘটে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব আন্দোলন বাঙালি সভ্যতাকেও ভারতীয় হিন্দু সভ্যতা থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। তাই, বাঙালির গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে আর্যাবর্তের বৈদিক ধর্ম থেকে পুরোপুরি আলাদা মনে করাই সংগত। ধর্মতত্ত্বের ইতিহাসে দেখা যায়, কোনো ধর্ম ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ না-থাকলেও প্রতিটি ধর্মের আবির্ভাব ঘটেছে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকায়, সেখানকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংকট সমস্যাকে কেন্দ্র করে। যেমন ইসলামের উদ্ভব হয়েছে আরবের মক্কায় হজরত মোহাম্মদের মাধ্যমে সেকালের ‘আইয়ামে জাহেলিয়াত’ থেকে মুক্তিকে কেন্দ্র করে। ঠিক তেমনই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মও এসেছে প্রাচীন বাংলার বাঙালি শ্রীচৈতন্যের মাধ্যমে তৎকালীন হিন্দুধর্মের চতুর্বর্ণ প্রথা, বিদেশি শাসকদের নিপীড়ন এবং হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের এলিটদের জোরজবরদস্তি থেকে ব্রাত্যজনের মুক্তির বার্তা নিয়ে।
বাংলায় চৈতনদেবের আন্দোলনে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা কেঁপে ওঠে। কেঁপে ওঠাই স্বাভাবিক। একদিকে হুসেন শাহর আমলে অন্ত্যজদের ইসলামপ্রীতি, অপরদিকে চৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেমে আকৃষ্ট হয়ে ছোটোজাতের মানুষগুলো বৈষ্ণবধর্মে ভিড়তে থাকল। চৈতন্যদেবের শোভাযাত্রা ক্রমশ দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতে থাকল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রত্যাখ্যান করে জাতপাতমুক্ত বৈষ্ণবধর্মে অন্ত্যজদের আত্মসমর্পণ। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা ক্ষেপে উঠলেন। কিছুটা দিশাহারাও। হয়ে উঠলেন। প্রতিহিংসাপরায়ণ। মাহাত্মের খবর্তায় ভীত-সন্ত্রস্ত। একদিকে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের দিকে ইসলাম ও বৈষ্ণব ধর্মে সাঁড়াশি আন্দোলন, অন্যদিকে বৈষ্ণব ধর্মের দিকে ইসলাম তথা রাজরোষ এবং ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রতিরোধ। উভয় সংকটের ধর্ম সংকট। চৈতন্যদেবের অন্তিম পর্ব সম্পর্কে যৌক্তিক বিদ্যায়তনিক সংশয় অপেক্ষা, অযৌক্তিক অপপ্রচারই বড়ো হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। সন্দেহ কেন? দুটি স্পষ্ট কারণ— (১) চৈতন্যদেবের মৃত্যু ঠিক কীভাবে হল সেই প্রশ্নের সঠিক উত্তর জানা নেই। এবং (২) শ্রীচৈতন্য জগন্নাথে মানে নীলাচলে লীন হয়ে গেলেন, এই প্রচার অনেকেই তাঁকে হত্যা করার সন্দেহই করছেন। জয়ানন্দের ‘পায়ে ইট লেগে মৃত্যু’-র তত্ত্ব বাস্তবে এক্কেবারেই অসম্ভব নয়। কিন্তু অন্যান্য কাব্যগুলি এই ভাবনাকে সমর্থন করে না বলে এ নিয়ে মানুষের সন্দেহ আছে। চৈতন্যদেবের ‘জগন্নাথে লীন হয়ে যাওয়ার বর্ণনা এই সন্দেহকে আরও জোরদার করেছে। অনেকের ধারণা পাণ্ডারা তাঁকে হত্যা করে এই প্রচার করেছে– মহাপ্রভু জগন্নাথে লীন হয়ে গেছেন! নিরঞ্জন ধর তাঁর ‘অবতার শ্রীচৈতন্য ও মানুষ নিমাই’ শিরোনামে একটি প্রবন্ধে যে কথা লিখেছেন, সেটি সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাক: ‘রাজরোষ’-এ পড়ে চৈতন্য নীলাচলবাসী হন এবং প্রতাপরুদ্রের সভাপতি নিযুক্ত হন। রাজরোষ’ থেকে নিজেকে রক্ষা করতেই নিমাই গৃহত্যাগী হন। মহানিষ্ক্রমণের রাতে নিমাই দুই বলবান মায় বিশ্বস্ত সহচর গদাধর ও হরিদাসকে নিজের দু-পাশে নিয়ে শুয়েছিলেন। এ ঘটনায় বোঝা যায়, নিমাই ওই রাতের অন্ধকারে সুলতানের লোকেরা তাঁকে ধরতে আসতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা করেছিলেন। ইতিমধ্যেই যে সুলতান তাঁর বিশ্বস্ত হিন্দু কর্মচারী কেশবছত্রীর উপর চৈতন্যকে ধরে আনার ভার দিয়েছেন। একথা শোনামাত্র সেদিনই রাতের অন্ধকারে তিনি ওই স্থান ত্যাগ করেন।
রাজশক্তির সঙ্গে প্রকাশ্যে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছিলেন নিমাই। নিমাই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন। সঙ্গে দণ্ড রাখতে শুরু করেন তিনি। চরম নিরাপত্তাহীনতার কারণে নিমাই নবদ্বীপ ছেড়ে পুরীতে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করতে মনস্থ করেন। কারণ একাধিক। প্রথমত ওড়িশা তখন পূর্ব ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী হিন্দুরাজ্য, তদুপরি বৈষ্ণব-প্রভাবিত ছিল। দ্বিতীয়ত পুরী বৈষ্ণবদের এক সর্বভারতীয় প্রধান তীর্থক্ষেত্র বটে এবং পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্ররা স্বয়ং ছিলেন বৈষ্ণবভাবাপন্ন। সর্বোপরি, নবদ্বীপবাসী যাঁরা মুসলিম শাসকদের অত্যাচারে ও নানা ফতোয়ায় অতিষ্ঠ হয়ে দেশত্যাগ করেছিলেন, তাঁরা প্রায় সকলেই পুরীতে এসে জমায়েত হয়েছিল। বাংলা-ওড়িশার সীমান্তের পরিস্থিতি কিছুটা অনুকূল থাকলেও চৈতন্য কোনো ঝুঁকি নেননি। তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর রামচন্দ্র খানের সঙ্গে তিনি আগে থেকেই আগাম বন্দোবস্ত করেছিলেন, যাতে তিনি নির্বিঘ্নে বাংলা-ওড়িশা সীমান্ত অতিক্রম করতে পারেন। তিনি বাংলার রাজরোষ অতিক্রম করে সীমান্ত পেরিয়ে ওড়িশায় প্রবেশ করলে এতটাই নিরাপদ বোধ করছিলেন যে, সর্বক্ষণের সঙ্গী তাঁর হস্তস্থিত দণ্ড সপাটে ভেঙে ফেলেন। কিন্তু শেষরক্ষা হল কোথায়! ওড়িশায় গিয়েও তিনি নোংরা রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। হ্যাঁ, চৈতন্য ওড়িশার অভ্যন্তরীণ রাজনীতির শিকার হয়েছিলেন। বস্তুত ওড়িশার সেদিনকার অভ্যন্তরীণ রাজনীতি পরিষ্কার দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। একদিকে প্রতাপরুদ্র ও চৈতন্যসম্প্রদায়, অপরদিকে বিদ্যাধর ও মন্দিরের পুরোহিতকুল।
উৎকলবাসীরা শ্রীচৈতন্যকে যখন ‘সচল জগন্নাথ’ ভাবতে শুরু করে দিয়েছেন, ঠিক সেই সময়কালে ঈর্ষান্বিত হয়ে ক্ষমতা দখলের চরম পর্যায়ের প্রস্তুতি হিসাবে গোবিন্দ বিদ্যাধর চৈতন্যশিবিরকে ছত্রখান করতে অগ্রসর হয়েছিলেন এবং জগন্নাথ মন্দিরের পুরোহিতকুলের সাহায্যপ্রার্থী হলেন। তাঁদের চৈতন্যবিরোধিতা তো ছিলই, উপরন্তু তাঁদেরকে আর্থিক টোপও দেওয়া হল। বলা হল– তীর্থযাত্রী, ভক্তদের কাছ থেকে পূজা-দান-প্রণামী ইত্যাদি বাবদ মন্দিরের যে বিরাট আয় হত তার সবটুকুই পুরোহিতদের প্রাপ্য। চৈতন্য যে এইসব ষড়যন্ত্র বুঝতে পারেননি তা নয়। তা বুঝেই কাশীশ্বর নামে এক ভীমদেহী ব্যক্তি অঙ্গরক্ষক রূপে সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন, যখন চৈতন্য মন্দির প্রদর্শনে আসতেন। যে দণ্ড তিনি সীমান্তে ভেঙে ফেলেছিলেন, তেমন দণ্ড তিনি আবার ধারণ করতে শুরু করলেন।
তবুও শেষ রক্ষা হয়নি। সেদিন ছিল জগন্নাথের চন্দন উৎসব। চন্দন সরোবরের চারপাশে দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়ছে। মন্দির প্রায় পরিত্যক্ত বলা যায়। কয়েকজন প্রহরী ও দু-একজন পুরোহিত মন্দির-প্রাঙ্গনে টুকটাক কাজে ব্যস্ত। এমন সময় সতর্ক পাহারা এড়িয়ে চৈতন্য একাকী মন্দিরে এসে উপস্থিত। তিনি মন্দিরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশপথগুলি বন্ধ করে দেওয়া হল। চৈতন্য অনুচরেরা দরজা খোলার জন্য দরজার বাইরে হইচই করতে থাকলেন, ভিতর থেকে কোনো সাড়া এলো না। বেশ কয়েক ঘণ্টা পরে দরজা খুলে মন্দিরের প্রহরী জানিয়ে দিল যে— চৈতন্য জগন্নাথের অংশ, জগন্নাথের দেহে মিশে গেছেন এবং তাঁর মৃতদেহ জগন্নাথের আদেশে ক্ষেত্রপাল আকাশ দিয়ে বয়ে নিয়ে গিয়ে গঙ্গায় বিসর্জন দিয়েছেন।
জগন্নাথ মন্দিরের পুরোহিতদের এহেন দুর্বল চিত্রনাট্য সরল ও শান্তিপ্রিয় বৈষ্ণবরা মাথা পেতে মেনে নিল বিনাবাক্যব্যয়ে। বৈষ্ণব তথা চৈতন্যভক্তগণরাও মনে করেন, ব্রাহ্মণ পাণ্ডারা চৈতন্যদেবের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। তদুপরি চৈতন্যদেবকে একা একা মন্দিরে যেতে নিষেধ করা হয়েছিল। রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্যদেবকে লিখিতভাবেই কড়া নিরাপত্তা দিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল, তাঁর মরদেহ কোথায় গেল –এসব প্রশ্নের উত্তর আজ আর নেই।
তবে অনেকেই মনে করেন মহাপ্রভু চৈতন্য অন্ত্যজদের উদ্ধার করার জন্য হরিনামে নগরকীর্তন করতেন না। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব আসলে ব্রাহ্মণ্যবাদ রক্ষার্থেই অন্ত্যজদের নিয়ে এই সংগঠন করেছিলেন। কারণ তখন বাংলায় ছিল হুসেন শাহর আমল এবং সুফিবাদের প্লাবন। এ সময়ে প্রচুর অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষরা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছিলেন। এই ধর্মান্তর স্রোতকে ঠেকাতেই ঘুর পথে অন্ত্যজদের ‘অস্পৃশ্য’ বলে ঘৃণা— এই অপবাদ এবং অপমানের অভিমানকে কাজে লাগিয়ে হিন্দুধর্মে ধরে রাখতে পারলেন তিনি, হিন্দুধর্মের শাখাধর্ম বৈষ্ণব ধর্মের আবরণে।
ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বশেষ ধর্মীয় আগ্রাসন এলো খ্রিস্টান মিশনারিদের হাত ধরে। টার্গেট আবার সেই অশিক্ষিত দলিত শ্রেণি। ব্রিটিশ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রেম ছড়াতে ছড়াতে খ্রিস্টান মিশনারিরাও ঢুকে পড়ল ভারতের মাটিতে। খ্রিস্টান মিশনারি খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের কাজে নিয়োজিত সংগঠন। প্রধানত প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ভুক্ত খ্রিস্টান মিশনারি উপনিবেশিক আমলে বাংলায় সক্রিয় থাকলেও তাঁদের সংযোগ স্থাপন শুরু হয় ষোলো শতকে। প্রারম্ভে জেসুইট ও রোমান ক্যাথলিকবৃন্দ একত্রে কাজ করেছেন এবং ১৫৯৯ খ্রিস্টাব্দে একটি গির্জা ও একটি মঠ স্থাপন করেন। ধর্মশিক্ষার জন্য একটি কনভেন্ট স্কুল ও সেন্ট পলের জেসুইট কলেজও প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৬২২ খ্রিস্টাব্দে সেইন্ট পল কলেজের রেক্টর হিসেবে ফাদার পিটার গোমেজের নিয়োগের মধ্য দিয়ে ধর্মসংক্রান্ত শিক্ষা কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে শুরু হয়। বি. রড্রিকস্, জেমস গোমেজ, সাইমন দি ফিগুরেডো ও আন্দ্রে ম্যাশাডো এটিকে শিক্ষাদান ও খ্রিস্টান ধর্মের সুসমাচার পৌঁছানোর একটি মহতী কেন্দ্রে পরিণত করেন। এক দশকের মধ্যে দশ হাজারের মতো ব্যক্তিকে ধর্মান্তরিত করা হয় বলে দাবি করা হয়। আঠারো শতকের শেষ দশকে ব্রিটিশ প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মপ্রচারকদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় তথা গোটা ভারতবর্ষে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচার কাজ একটি সংগঠিত আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। সমসাময়িক ইংল্যান্ডে প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের পুনরুজ্জীবনের ফলে সকল দেশে খ্রিস্টের বাণী প্রচারের জন্য বেশ কয়েকটি ধর্মপ্রচারক সমিতি গঠিত হয়। এগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল ১৭৯২, ১৭৯৫ ও ১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত যথাক্রমে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটি, লন্ডন মিশনারি সোসাইটি ও চার্চ মিশনারি সোসাইটি। কয়েক দশক পর ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে আলেকজান্ডার ডাফ (১৮০৮-১৮৭৮)-এর অধীনে স্কটল্যান্ডের গির্জা বাংলায় ধর্মপ্রচার কাজ শুরু করে। কিন্তু এ সকল গির্জা বাংলায় ধর্মপ্রচার কাজ চালানোর ক্ষেত্রে প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ভুক্ত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়। স্কটিশ ধর্মপ্রচারকগণ ও আইরিশদের গির্জার যাজকীয় শাসনতন্ত্রের সমর্থকবৃন্দও এ কার্যক্রম অনুসরণ করেছিলেন। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা উনিশ শতককে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারের বিশিষ্টতম শতকে রূপান্তরিত করে।
খ্রিস্টান ধর্ম ও উপমহাদেশের ধর্মসমূহের মধ্যকার সাংস্কৃতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকগণ ইসলামের অনুসারীদের প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হন, সম্ভবত। একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী মুসলিমগণ খ্রিস্টান ধর্মের ‘ত্রিত্ববাদী’ মতবাদকে গ্রহণ করতে পারেনি। সাধারণভাবে মুসলিম সমাজ খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের প্রচেষ্টার আওতার বাইরে থেকে যায় এবং মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামীণ পূর্ববঙ্গে খুব অল্প কয়েকটি ধর্মপ্রচার কেন্দ্র গড়ে ওঠেছিল। শ্রীরামপুর এয়ী কিছু হিন্দু সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও আচারানুষ্ঠান, যেমন জাতিভেদ প্রথা, সতীদাহ, সন্তানকে গঙ্গায় বিসর্জন, অন্তৰ্জলি ইত্যাদি সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে জনমত গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। ১৮০৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দের এই মাঝের সময়টুকুতে এ রকম কিছু আচারকে নিষিদ্ধ করতে আইন পাসে তাঁরা সহায়ক ছিলেন। সাঁওতাল মিশনে জর্জ ক্যাম্বেলের গভীর আগ্রহ এবং সাঁওতালদের শিক্ষার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুদান ধর্মপ্রচারকদের অনুপ্রাণিত করে। উনিশ শতকের শেষ নাগাদ সাঁওতালদের শিক্ষিত করে তোলার কাজ একচেটিয়াভাবে ধর্মপ্রচারক সমিতিগুলির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের প্রধান উদ্দেশ্য, যা ছিল খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার মাধ্যমে বাংলার মানবগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন সাধন করা, কখনও পূরণ হয়নি। তাঁদের ভবিষ্যৎ অনেকটা নির্ভর করত জাতিচ্যুত ও উপজাতিদের ধর্মান্তরকরণের মধ্য দিয়েই। চার্চ ও ব্যাপ্টিস্ট মিশনসমূহের সর্বাধিক সংখ্যক ধর্মান্তরিতগণ আসত কর্তাভজাদের (ঈশ্বরের পূজারী) মধ্য থেকে, যাঁরা ছিল ‘নিম্নবর্গ’ পদমর্যাদার হিন্দু, যেমন চণ্ডাল ও নমঃশূদ্রদের মধ্যে গড়ে ওঠতে থাকা একটি হিন্দু সমতাবাদী ধর্মীয় সম্প্রদায়। সমাজের দরিদ্র মানুষের সেবা করার ছলে তাঁরা গরিব হিন্দু-মুসলমানদের খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করে আসছে, আজও যা অব্যাহত। খ্রিস্টান মিশনারিরা এমন সব জায়গায় যায় যেখানকার মানুষগুলো খুবই দরিদ্র, অশিক্ষিত এবং অবশ্যই দলিত শ্রেণির। খ্রিস্টান মিশনারির কর্মচারীরা এমন লোক খুঁজে বেড়ায় যাঁরা ঋণ নিয়ে পরিশোধ করতে পারছে না, অসুস্থ টাকার অভাবে চিকিৎসা করাতে পারছে না, টাকার অভাবে না খেয়ে মরে যাওয়ার অবস্থা— এককথায় অভাবী এবং সমাজে ঘৃণিত মানুষদের খুঁজে বেড়ায়। খ্রিস্টান মিশনারিরা এই সুযোগে তাঁদের টাকা দিয়ে সাহায্য করে, আর সাহায্য করার ছলে ধর্মের প্রচার এবং ধর্মান্তর করতে থাকে। এদের টার্গেট দলিত, দরিদ্র এবং অনাথ। বিভিন্ন দেশের দরিদ্র এবং অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী খুব সহজেই তাঁদের ছলনায় চিন্তা করে হিন্দু অথবা মুসলমান হয়ে তো কোনো লাভ নেই। তাঁরা মনে করেন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলে তাঁদের অনেক সুবিধা, তাঁদের সমস্ত অভাব দূর হয়ে যাবে। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত ছিল পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম খ্রিস্টধর্মী দেশ। ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে তা পঞ্চমে উন্নীত হবে (সূত্র : www.worldchristiandatabase.org)। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে ভারত ছিল পৃথিবী দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ। যা ২০২৫ খ্রিস্টাব্দে তৃতীয়তে চলে যাবে (সূত্র : www.worldchristiandatabase.org)। মজার বিষয় হল– বৌদ্ধ, ইসলাম, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা যতটা অসহিষ্ণু ছিলেন, খ্রিস্টান মিশনারিদের ক্ষেত্রে ঠিক ততটাই সহিষ্ণু কেন! দলিতদের খ্রিস্টধর্মে চলে যাওয়ার ঘটনায় ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এত উদাসীন ছিলেন কেন! ইংরেজপ্রীতি, নাকি অন্য কোনো মতলব! ইংরেজপ্রীতি যে ছিলই সেটা ব্রিটিশ ভারত ইতিহাসের পরতে পরতে চিহ্ন রাখা আছে। মানবসেবা, সমাজসেবার নামে দিনের পর দিন অতীতে মাদার টেরিজা চালিয়েছিলেন, বর্তমানে স্টিভ ‘ও সহ অনেকেই ধর্মান্তরের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন ছলে আর কৌশলে! এই ধর্মান্তরযজ্ঞের জন্য কোটি কোটি ডলার আসছে বিদেশ থেকে।
কেউ কেউ বলেন জাতপাতের এই বিড়ম্বনা নাকি হিন্দুধর্মের নয়। হিন্দুধর্মে নাকি জাত-বিভাজনের বালাই নেই –এসব নাকি ব্রাহ্মণ্যধর্মের হিন্দুদের ঘাড়ের চাপিয়ে দেওয়া নিষ্পেষণ-চাক্কি। তাহলে কি ব্রাহ্মণ্যধর্ম আর হিন্দুধর্ম সমার্থক নয়! এ ভাবনার যুক্তি কী? তাঁরা বলছেন– (১) তাঁদের প্রত্যেকের ধর্মপালনের নীতি-নিয়ম একই হবে। (২) তাঁরা একই পদ্ধতিতে ধর্মাচরণ বা উপাসনা করবে। (৩) তাঁদের মধ্যে অবাধ বিবাহ সম্পর্ক চালু থাকবে। (৪) ধর্মের দৃষ্টিতে তাঁরা সবাই অভিন্ন বলে বিবেচিত হবে। (৫) তাঁদের মধ্যে কোনো উঁচু-নীচু ভেদ থাকবে না। (৬) তাঁরা সবাই সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। থাকবে। (৭) একই ধর্মের অনুগামী বলে তাঁরা পরস্পরের প্রতি একাত্মবোধ করবে। এই বৈশিষ্ট্যগুলি ব্রাহ্মণ ও হিন্দুর ক্ষেত্রে এক নয়, আলাদা। এ পরিপ্রেক্ষিত বিচার করে বোঝা যায় ব্রাহ্মণ ও হিন্দু এক ধর্মভুক্ত নয়, তাঁদের ধর্ম আলাদা। তা ছাড়া দুটি আলাদা ধর্মের মানবগোষ্ঠীর মধ্যে যে বৈসাদৃশ্যগুলি থাকে ব্রাহ্মণ ও হিন্দুর মধ্যেও তা লক্ষ করা যায়। বৈসাদৃশ্যগুলি মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে, যেমন— (১) ব্রাহ্মণ ও হিন্দুর মধ্যে বিবাহ সম্পর্ক হয় না। যদিও কিছু ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায়, তবে ব্যতিক্রম ব্যতিক্রমই। (২) ব্রাহ্মণ ও হিন্দুর মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের ভাব দেখা যায় না, বরং ঘৃণার সম্পর্ক দেখা যায়। (৩) একজন ব্রাহ্মণ ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে যে অধিকার পায়, একজন হিন্দু তা পায় না। (৪) ব্রাহ্মণ ও হিন্দু পরস্পরের সঙ্গে একাত্ম মনে করে না। (৫) ব্রাহ্মণ হিন্দুকে তাঁর সঙ্গে সমমর্যাদার ভাবে না, তাঁর থেকে নীচু ভাবে। (৬) ব্রাহ্মণদের ধর্মপালনের উদ্দেশ্য শূদ্রদের সম্পদ হাতানো। হিন্দুদের ধর্মপালনের উদ্দেশ্য সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। (৭) ব্রাহ্মণ্যধর্মে অব্রাহ্মণ আছে এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের এই অব্রাহ্মণরা হল পথভ্রান্ত, নিজের অজান্তে বিপথে চালিত ধর্মচ্যুত হিন্দু, ব্রাহ্মণরা যাঁদের উপর অপমানজনক, ঘৃণ্য ‘শূদ্র’ নামের ছাপ্পা মেরে দিয়েছে। কিন্তু হিন্দুধর্মে কোনো অহিন্দু নেই। (৮) ব্রাহ্মণ্যধর্ম অনুযায়ী ব্রাহ্মণ সবার শ্রেষ্ঠ, সবার প্রভু। আর ব্রাহ্মণ্যধর্ম অনুগামী অব্রাহ্মণরা ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিকৃষ্ট, এমনকি কেউ কেউ আবার ব্রাহ্মণদের নিকট ঘৃণার বস্তু, অস্পৃশ্য। কিন্তু হিন্দু ধর্মে কোনো উচ্চনীচ ভেদাভেদ নেই, সবাই সমান। (৯) বর্ণভেদ, জাতপাত, অস্পৃশ্যতা, সতীদাহপ্রথা, গুরুপ্রসাদী প্রথা ইত্যাদি অমানবিক, অশালীন প্রথাগুলি ব্রাহ্মণ্যধর্মেরই অবদান। কিন্তু অপরদিকে হিন্দুধর্ম একটি সুসভ্য, যুক্তিবাদী ও মানবতাবাদী ধর্ম। (১০) ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুগামীরা সবাই ব্রাহ্মণ নয়, কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ শূদ্র ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু হিন্দুধর্মের অনুগামী মাত্রেই সবাই হিন্দু এবং কেবলমাত্র হিন্দু। হিন্দুদের একমাত্র পরিচয়— তাঁরা হিন্দু। (১১) ব্রাহ্মণদের উপনয়ন হয়, হিন্দুদের হয় না। (১২) ব্রাহ্মণ্যধর্মে জাতপাত, বর্ণভেদ, অস্পৃশ্যতা আছে, কিন্তু হিন্দুধর্মে ওইসব কদর্য জিনিস নেই। ওগুলো সম্পূর্ণতই ব্রাহ্মণ্যধর্মের ব্যাপার, হিন্দুধর্মের নয়। (১৩) ব্রাহ্মণরা পৈতে পরে, কিন্তু হিন্দুরা তা পরে না। তাই পৈতে পরা দেখে ব্রাহ্মণকে সহজেই স্বতন্ত্র ধর্মের অনুগামী হিসাবে সনাক্ত করা যায়— যেমন টুপি (ফেজ) পরা দেখে সহি মুসলমানদের সনাক্ত করা যায়, বুকে ক্রুশ দেখে খ্রিস্টান সনাক্ত।
এইসব তথ্য বিচার ও বিশ্লেষণ করলে সহজেই অনুমিত হয় যে, ব্রাহ্মণ্য ও হিন্দু দুটি স্বতন্ত্র ধর্ম, কখনোই এক ধর্ম নয়। অতএব ব্রাহ্মণ্যবাদের সব রকম অন্যায়-অবিচার হিন্দুধর্মের উপর চাপিয়ে দেওয়াটা সুবিচার হয় না। এ ব্যাপারে শিবরাম চক্রবর্তীর বক্তব্য অনুধাবনযোগ্য— “এই হিন্দু সভ্যতায় ব্রাহ্মণের দান অতি সামান্যই, বলতে গেলে ব্রাহ্মণের থেকে যতটা এ নিয়েছে –তাই এর কলঙ্ক। ……ব্রাহ্মণের দ্বারা প্রভাবিত না হলে এ সভ্যতা আরও প্রাণবান, আরও বেগবান, আরও বীর্যবান হতে পারত। …… ব্রাহ্মণ্য সভ্যতার চেয়ে ঢের বড়ো এই হিন্দু সভ্যতা। ব্রাহ্মণ না জন্মালেও এ হত এবং ব্রাহ্মণ লোপ পেলেও হিন্দু সভ্যতা থাকবে।….. ব্রাহ্মণরা সমাজের মাথা নয়, বরং টিকি। সমাজের মাথা থেকে ওটাকে কেটে বাদ দিলে সমাজটার কোনো ক্ষতি হবে না, বরং তাকে আরও বেশি আধুনিক দেখাবে।”
সেই কারণেই বোধহয় অন্ত্যজ বা দলিতদের সম্মানের জন্য যাঁরা লড়াই করেছেন এবং করছেন, তাঁরা সকলেই প্রায় উচ্চবর্ণের হিন্দু। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ, স্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধি প্রমুখ উচ্চবর্ণীয় ব্যক্তিগণ দলিতদের পক্ষে জোরদার আন্দোলন করেছেন। অবশ্য ড: ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের আন্দোলনও দলিত সমাজে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও বাবা আহম্মেদকর উচ্চবংশীয় ছিলেন না, বরং তিনি দলিত শ্রেণির। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর বর্তমান ভারত’ গ্রন্থে লিখেছেন– “ভারতবাসীর কেবল ভারবাহী পশুত্ব, কেবল শূদ্রত্ব।” বিবেকানন্দের সমকালীন। ভারতে ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্বের অধিকারী হলেন ইংরেজ এবং তাঁদের শাসন-শোষণের ভার পশুর মতো বহন করে চলেছে শূদ্ররূপ ভারতবাসী। বিবেকানন্দ মনে করতেন, “শূদ্রজাতি মাত্রেই এজন্য নৈসর্গিক নিয়মে পরাধীন।”
ব্রাহ্মণ্যবাদী স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর ‘শূদ্র জাগরণ’ প্রবন্ধে লিখেছেন– “ব্যক্তিবিশেষ ইংরেজ কৃষ্ণবর্ণ বা নেটিভ অর্থাৎ অসভ্য বলিয়া আমাদিগকে অবজ্ঞা করিলে, ইহাতে ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই, আমাদের আপনার মধ্যে তদপেক্ষা অনেক অধিক জাতিগত ঘৃণাবুদ্ধি আছে; এবং মূর্খ ক্ষত্রিয় রাজা সহায় হইলে ব্রাহ্মণেরা যে শূদ্রদের জিহ্বচ্ছেদ, শরীরভেদাদি পুনরায় করিবার চেষ্টা করিবেন না কে বলিতে পারে?”
‘দলিত’ কথাটির অর্থ এমন বস্তু বা মানুষ যাঁদের কেটে ফেলা হয়েছে, ভেঙে দেওয়া হয়েছে, টুকরো টুকরো করে পিষে ফেলা হয়েছে এবং ধ্বংস করা হয়েছে। মারাঠি সমাজসংস্কারক ও বিপ্লবী মহাত্মা জ্যোতিবা ফুলে হিন্দু সমাজে নিপীড়িত অবর্ণ ও অস্পৃশ্য জাতিগুলির ক্ষেত্রে এই কথাটি ব্যবহার করেন। সাধারণভাবে ‘দলিত’ কথাটির অর্থ নিম্নবর্ণ বা দরিদ্র নয়, বরং এই শব্দটি দিয়ে বোঝানো হচ্ছে এক অবদমিত অবস্থা। সামাজিক রীতি তাঁদের যে অধঃপতিত করেছে দলিত বলতে সেটাই বোঝাচ্ছে। যাঁদের দলন করা হয় তাঁরাই দলিত। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয় যে, যাঁরা নিচু কাজ করে তাঁরা পুনর্জন্মে খারাপ জন্ম পায়। তাঁরা কুকুর বা শুয়োর বা চণ্ডাল হিসাবে জন্মায়। এই অস্পৃশ্য দলিত/শূদ্রদেরই মহাত্মা গান্ধি বললেন ‘হরিজন’। তিনি ‘হরিজন’ নামে একটি সংবাদপত্র করতেন এবং হরিজনদের বিষয়ে লেখালেখি করতেন। সে সময়েও শূদ্ররা শুধু অস্পৃশ্যই ছিলেন না, তাঁদের ছায়া পর্যন্ত পড়তে পারত না ব্রাহ্মণদের শরীরে। ব্রাহ্মণরা যে পথে চলবেন সে পথে শূদ্রদের চলন গর্হিত অপরাধ। ব্রাহ্মণদের সামনে শূদ্রদের ছাতা মাথায় বুক চিতিয়ে যাওয়াটা চরম ধৃষ্টতা। শূদ্র, অর্থাৎ অস্পৃশ্যদের কোনো দেবতা নেই। দেবতা নেই, দেউলও নেই। এইসব অস্পৃশ্যদের কোনো মন্দিরে প্রবেশ করার অধিকার ছিল না। অপবিত্র হয়ে যাবে দেব ও দেউল। একই কুয়োয় জল ব্যবহারের অধিকার ছিল না। শূদ্ররা যেখানে বসে সেখান থেকে চলে যাওয়ার পর গৃহস্থ গঙ্গাজল গোবরজল ছিটাবে। গান্ধিজি ব্রাহ্মণ্যধর্মের এই অমানবিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন। মহাত্মা গান্ধিজি অস্পৃশ্য হরিজনদের হাতে ‘অনুগ্রহণ আন্দোলন’-এর প্রথম সারির উদ্যোক্তা ছিলেন। তা সত্ত্বেও বলা যায়, মহাত্মা গান্ধি শূদ্রদের জন্য তেমন কিছু করে উঠতে পারেননি। তিনি সকলের কাছে ‘বাপুজি’ হতে সক্ষম হলেও শেষপর্যন্ত শূদ্রদের বাপুজি হতে পারেননি। অস্পৃশ্য শূদ্রদের নতুন নাম হরিজন’ দিলেন বটে, কিন্ত একবিন্দু মর্যাদা দিতে পারেননি। নাম বদলালেই মর্যাদা বদলায় না। হরিজন কেন? এই হরি কি ঈশ্বর হরি? তাই যদি হয় হরি তো সকলেরই ঈশ্বর; হরিজন তো সকলেই। তাহলে কেন শূদ্রদেরই কেবল হরিজন বলা হচ্ছে। তাঁদেরকে কি হরি আলাদাভাবে জন্ম দিয়েছেন? উচ্চবর্ণের হরি আর নিম্নবর্ণের হরি কি আলাদা? হরিজন মানে যদি ঈশ্বরের সন্তান হয় তাহলে দলিত ছাড়া বাকিরা কার সন্তান?
আসলে প্রকারান্তরে গান্ধিজি ব্রাহ্মণ্যধর্মের সৃষ্ট বর্ণবৈষম্যকে স্বীকার করে নিয়েছেন। উনি উপলব্ধি করেছেন বর্ণপ্রথার প্রয়োজন আছে। যদিও তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন না, কিন্তু দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে ব্রাহ্মণরাই তাঁকে ঘিরে থাকতেন। তদুপরি, তিনি কোনো শূদ্রের সঙ্গে আত্মীয়তা সম্পর্ক গড়েছেন বলে জানা নেই। গান্ধিজি ভারতের ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে যেতে পারেননি। বলা যায় গান্ধিজি ব্রাহ্মণ্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, ব্রাহ্মণ্যবাদে বিশ্বাস অটুট রেখে শূদ্রদের মঙ্গল করা সম্ভব নয়। হয়ওনি। গান্ধিজি যদি আন্তরিকভাবেই শূদ্রদের মর্যাদাই চাইতেন তাহলে এত সময় রাজনীতিতে ব্যয় না-করে ভারতের দলিত অর্থাৎ পিছড়ে বৰ্গদের অধিকার আদায়ের কাজে লাগাতার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে পারতেন। তিনি বদলে দিতে পারতেন ভারতের ইতিহাসের ধারা। তৈরি হতে পারত নতুন এক ভারত। মুছে যেত ব্রাহ্মণ-শূদ্রের স্বতন্ত্র পরিচয়। তিনি শূদ্রদের ‘হরিজন’ শিরোপা দিয়ে সকলকেই যদি ‘হিন্দু হতে বলতেন, তাহলে সব ব্রাহ্মণ না-এলেও অনেকেই দলিত/শূদ্রদের পাশে এসে দাঁড়াতেন। তাহলে আজকের দিনেও কোনো উচ্চবর্ণের সাহস হত না একটি দলিতকেও নগ্ন করতে। bjpwb indiawb ফেসবুক পেজ থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা একথা লিখতে সাহস পেত– “কিছুদিন পরে আমরা পুরো ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবাংলায় শাসন করব, তখন মুসলিম-আদিবাসী-খ্রিস্টান সকলকে হিন্দুধর্মে রূপান্তরিত করব, না-হলে ঘরে ঢুকে এক এক করে হত্যা করব। এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। এরই নাম হিন্দুত্ব এবং হিন্দুরাষ্ট্র”? এই পেজেই আর-একটি পোস্টে বলা হয়েছে– “সামনের ইলেকশনে টিএমসি, সিপিএম এবং অন্যান্য দলগুলিকে একতরফা হারিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবাংলায় সরকার গঠন করবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে মুল্লাদের, খ্রিস্টানদের, আদিবাসী ও দলিতদের পশ্চিমবঙ্গ থেকে চলে যাওয়া লাগবে।” বিজেপির বিধায়ক রাজা সিংহও বলতে সাহস পায়– “দলিতোঁ কি পিটাই সে খুশি মিলতি হ্যায়”। দলিত তথা আদিবাসীরা কি হিন্দু নয়? তাই যদি হয়, এই হিন্দুধর্মকে রক্ষা করার কোনো পথই খোলা রইল না। দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্যবাদীরা হিন্দুধর্মের যে সর্বনাশ করার কাজ হাতে নিয়েছিল, এই বাণীগুলি কি একবিংশ শতাব্দীতেই অন্তিমপর্ব চলছে?
দেবদাসী প্রথা দক্ষিণ ভারতে এখনও টিকে আছে। এসব দেবদাসীরা অধিকাংশই হরিজন সম্প্রদায়ের থেকে আসা। ব্রাহ্মণরা তাঁদের দিনের পর দিন ভোগ করলে জাত যায় না। জাত যায় তাঁদের হাতের জল খেলে। দলিত হরিজনরা এখনও মূলস্রোতের সঙ্গে মিশতে পারেনি। ফলে তাঁরা কলোনিভিত্তিক জীবনযাপন করে যাচ্ছে ব্যাপক অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে। দলিত-হরিজনরা যেন অস্পৃশ্য। দলিত সম্প্রদায় জন্ম ও পেশাগত কারণে বৈষম্য এবং বঞ্চনার শিকার মানুষরা আন্তর্জাতিক পরিসরে বিশেষ করে পণ্ডিতদের কাছে ‘দলিত’ নামে পরিচিতি পায়।
এক ঈশ্বরের সৃষ্টি, এক ধর্মালম্বী, একই নিয়মে পিতা-মাতার মাধ্যমে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে এত জাতিগত বৈষম্য কেন? নিশ্চয় এটা বিধির বিধান নয়, এটা সম্পূর্ণ মানুষের (ব্রাহ্মণের) তৈরি জাতিভেদের দলিল মাত্র, এতে কোনো সন্দেহ নেই। এ ছাড়াও এক জাতি বা বর্ণের পুরুষের ঔরসে অন্য জাতি বা বর্ণের নারীর গর্ভে সন্তান জন্ম হলে শাস্ত্র বিধান মতে তাঁদেরকে অস্পৃশ্য, পতিত, জারজ, নীচু জাতি বা বর্ণ শঙ্কর বলা হত এবং এঁদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ তথা উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অমানবিক আচরণ করত। যেমন ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্য নারীর গর্ভে বাগদির জন্ম, এরা অস্পৃশ্য বা পতিত জাতি। শূদ্রের ঔরসে দ্বিজ (ব্রাহ্মণ) রমণীর গর্ভে চণ্ডালের জন্ম, এঁরা জারজ দোষে পতিত বা অস্পৃশ্য।
এইভাবে ছত্রিশ বর্ণ বা জাতির উৎপত্তি, এরূপ বহু ছোটো জাত বা অস্পৃশ্য জাতির উল্লেখ আছে (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড, ৫৯ পৃষ্ঠা)। হিন্দুধর্মে পালনীয় অপস্তম্ব ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে, কেউ চণ্ডালকে স্পর্শ করলে তাঁকে জলে স্নান করতে হবে। কেউ চণ্ডালের সঙ্গে কথা বললে তারপর ব্রাহ্মণের সঙ্গে কথা বলতে হবে। চণ্ডালের উপরে চোখ পড়লে তারপর আকাশের সূর্য, চন্দ্র, তারার দিকে তাকিয়ে চোখ শুদ্ধ করে নিতে হবে। পরাশর স্মৃতিতে বর্ণিত হয়েছে আরও কঠোরতা। বলছে, কোনো দ্বিজ অনুগ্রহণের সময় কোনো কুকুর বা চণ্ডাল যদি তাঁকে স্পর্শ করে তাহলে সেই খাদ্য ফেলে দিতে হবে। চণ্ডালের ছোঁয়া কুয়ো থেকে কোনো ব্রাহ্মণ যদি জলপান করে তাহলে তাঁকে তিনদিন ধরে গোমূত্র মেশানো যব খেতে হবে। কারও ঘরে যদি চণ্ডাল প্রবেশ করে তবে গোবর মেশানো জল দিয়ে সমস্ত ঘর ধুয়ে ফেলতে হবে। মাটির হাঁড়িকুড়ি ফেলে দিতে হবে। বাড়ির পরিচারক সহ পরিবারের লোকেরা দিনে তিনবার করে গোমূত্র মিশ্রিত ঘোল খাবে। পরের তিনদিন গোমূত্র মিশ্রিত যবের জল খাবে। তারপরের তিনদিন গোমূত্র মিশ্রিত দুধ খাবে। তারপর এইসব মিশ্রণ একদিন করে খেতে হবে। এইভাবে বারো দিন ধরে শুদ্ধিকরণ চলবে। নারদের মতে –শ্বপাক, মেদ, চণ্ডাল ও মালারা ছিল মনুষ্য সমাজের বর্জ। তাঁদের জন্য মৃত্যুদণ্ডই ভালো, কেননা অর্থদণ্ড করলে তাঁদের ছোঁয়া অর্থ নেওয়া যাবে না। তাঁদের অর্থও দূষিত (নারদস্মৃতি, পৃষ্ঠা ৪১)। কী তীব্র ঘৃণা, ভাবুন! কোনো একটা ধর্মগ্রন্থ নয়, বরং যুগ যুগ ধরে কীভাবে হিন্দুসমাজ অস্পৃশ্যতার ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল সেটা বোঝা যায়। আসলে এই হল সনাতন ধর্ম, যে চিরন্তন এইভাবে।
হিন্দুসমাজের এক সময়কার রাজা বল্লালসেন সমাজের মহা সর্বনাশ করেছেন। যতদিন এই পৃথিবী থাকবে ততদিন বল্লালসেনের অনাচার ও অনাসৃষ্টি হিন্দু সমাজ ভুলবে না। তিনি ছিলেন ধর্মে বৌদ্ধ এবং তাঁর গুরু ভট্ট-পাদ সিংহগিরি তাঁকে দীক্ষা দিয়ে শৈব মতে আনলেন। বাংলার রাজা বল্লালসেন বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করে হলায়ুদ উমাপতি নামে দুই ব্রাহ্মণের সাহায্য চান। হলায়ুদ বল্লালের মন্ত্রী ও উমাপতি তাঁর পঞ্চরত্নের অন্যতম ছিলেন। এঁদের সাহায্যে বল্লাল সেন ছলে-বলে-কৌশলে বঙ্গে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য স্থাপন করেন। ব্রাহ্মণের বশতা স্বীকার করার নাম ব্রাহ্মণ্যধর্ম। ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের ফলে অনেক মানুষ হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেন। বল্লাল সেন বৌদ্ধধর্ম উচ্ছেদ করেন এবং দ্বেষ, ঈর্ষা, স্বার্থপূর্ণ নৈতিকতাহীন ব্রাহ্মণধর্ম প্রচারে নিবেদিত হলেন। যার ফলে এ বঙ্গে শত শত জাতি ও উপজাতির সৃষ্টি হল। আত্মকলহ, ঝগড়া-বিবাদ, হিংসা, ঘৃণায় জাতি অসার ও বলহীন হয়ে পড়ল।
যে সকল জনসাধারণ রাজার ও ব্রাহ্মণদের নিয়মনীতি মানল না তাঁদের পতিত ঘোষণা করা হল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের দেওয়া ঘুষের মহিমায় শাস্ত্রের নামে জালিয়াতি করে প্রচার করল– ব্রাহ্মণ বাদে বাকি সকল মানুষই শূদ্র। সকলেই হীন, নীচ,পতিত, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য ও বর্ণ সঙ্কর।
‘পরশুরামসংহিতা’ নামক একটি গ্রন্থে শূদ্রবিদ্বেষী ব্রাহ্মণেরা প্রচার করলেন, বারুজীবীর বীর্যে তেলি, কর্মকারের বীর্যে মালাকার, গোপের বীর্যে বারুজীবী, তেলির বীর্যে কর্মকার, মালাকারের বীর্যে পট্টিকার, পট্টিকারের দ্বারা কুম্ভকার, কুম্ভকারের দ্বারা কুবেরী এবং কুবেরীর দ্বারা নাপিতের জন্ম হয়েছে। মনুসংহিতা এবং মহাভারতের মধ্য দিয়ে প্রচার করা হল ক্ষত্রিয়-স্বামী ও ব্রাহ্মণী-স্ত্রীতে মিলনের ফলে সূত জাতি জন্ম (সূত জাতি যে কত ঘৃণ্য তা মহাভারতে প্রতিফলিত হল কর্ণের মধ্য। স্বয়ংবর সভায় কর্ণকে সূতপুত্র বলে চরম অপমান করা হল। সূতপুত্র বলে তাঁকে স্বয়ংবর সভায় অংশগ্রহণ করতেই দেওয়া হল না। যদিও কর্ণ ছিলেন ক্ষত্রিয়ের সন্তান। কুন্তি ও সূর্যের সন্তান। সে সম্পর্ক গোপন রাখা হয়েছিল কুন্তী কুমারী থাকাকালীন কর্ণকে জন্ম দিয়েছিলেন। ফলে এই অবৈধ সন্তান কর্ণকে জলে ভাসিয়ে দিতে হয়েছিল। সেই সন্তানকে বড়ো করে তোলেন অধিরথ ও তাঁর স্ত্রী রাধা। সূত সম্প্রদায়ের অধিরথ ছিলেন ভীষ্মের সারথী।)।
বৈশ্য-স্বামী ও ক্ষত্রিয়-স্ত্রীতে মাগধ জাতির জন্ম। বৈশ্য-স্বামী ও ব্রাহ্মণী স্ত্রীতে বৈদেহ জাতির জন্ম। (মনুসংহিতা : ১০/১১, মহাভারত : অনুশাসন ৪৮/১০)। কিন্তু পৌরাণিক কাহিনিতে এসে অন্য প্রকার তথ্য পাই। পিতা জমদগ্নি ব্রাহ্মণ, মাতা রেণুকা ক্ষত্রিয় কন্যা— পুত্র জন্মালেন পরশুরাম। তিনি সূত না-হয়ে ব্রাহ্মণ হলেন। কোথাও কোথাও প্রচার হল শূদ্র পিতা ও ব্রাহ্মণী মাতাতে যে সন্তান হয় সেই সন্তান হয় চণ্ডাল। মগধের রাজা বিন্দুসার শূদ্র, বিবাহ করেন এক ব্রাহ্মণীকে— পুত্র হলেন বিশ্বখ্যাত ক্ষত্রিয় রাজা অশোক। অশোক পণ্ডিতদের তৈরি শ্লোকের প্রভাবে চণ্ডাল হননি। বল্লালসেন সকলের দ্বিজত্ব উঠিয়ে দিয়ে ব্রাহ্মণবাদের সকল হিন্দুদের শূদ্র নামে ঘোষিত করেন। মাহিষ্যরা ছিলেন বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়। মহারাজ কার্তবীর্যাজুন এঁদের পূর্বপুরুষ। ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এঁদের বহুকাল যুদ্ধ-সংঘর্ষ হয়। বৌদ্ধযুগের একদল সন্ত, সাঁই বা সাধু বল্লালসেনের অত্যাচার সহ্য করতে না-পেরে বিহারের পাহাড়ে আশ্রয় নেন। এঁরাই পরে সাঁইতার বা সাঁওতাল নামে খ্যাত হন। শঙ্খনির্মিত অলংকার বিক্রেতা শাঁখারী বা শঙ্খবণিক, কাঁশারী, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিকেরা ব্রাহ্মণ ছিলেন। বল্লালসেন এঁদের পৈতা ছিঁড়ে ফেলে শূদ্র ঘোষণা করে দেন। সূত্রধরেরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। এভাবে রাজা বল্লালসেনের অত্যাচারে তেওর, জালিক, রজক, দুলে, বেহারা, কেওরা প্রভৃতি অনেকেই বৈশ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেও বল্লালসেনের ফতোয়ায় সকলেই শূদ্র হতে বাধ্য হন। বল্লালসেন যেসব ব্রাহ্মণ, বৈশ্য এবং ক্ষত্রিয়কে জোর করে শূদ্র করেন তাঁদের গৃহে পৌরহিত্য করতে অন্য ব্রাহ্মণদের নিষেধ করে দিলেন। বল্লালসেনের অত্যাচারে হিংসা ও নীচতায় এ বঙ্গে হিন্দুসমাজের মেরুদণ্ড ঠুনকো হয়ে গেল। হাজার হাজার ব্রাহ্মণের পৈতা জোর করে ছিঁড়ে তাঁদের শূদ্র ঘোষণা করলেন এবং অনেক পদলেহী শূদ্রকে তিনি ব্রাহ্মণ উপাধি দিলেন।
আচার্য সুভাষ শাস্ত্রী বলেন, “ভ্রষ্ট চরিত্রের বল্লাল সেন এক বিবাহিতা ডোম কন্যাকে জোর করে তুলে এনে বিয়ে করেন এবং তাঁর কৃত পাপ অর্থ সম্পদ দ্বারা হিন্দু সমাজের সমাজপতি ও পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করলেন। পার্বত্য ডোমজাতি বল্লালসেনের ছোঁয়ায় ব্রাহ্মণ জাতিতে পরিণত হল। বল্লালসেনের চরিত্র ছিল নারীহরণ ও ব্যাভিচার দোষে কলুষিত। যেসব ব্রাহ্মণগণ তাঁকে মান্য করলেন তিনি তাদের কুলীন উপাধি দিলেন। … ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও শূদ্রের মুণ্ডপাত করে নিজের পাপাচার ও ক্ষমতাকে হিন্দুসমাজের মধ্যে স্থায়ী আসন দেওয়ার জন্য তাঁর পোষা পুরোহিতদের ব্যবহার করেন এবং হিন্দুসমাজের মধ্যে বর্তমান বিভেদ-বৈষম্য, ছুৎমার্গ, অস্পৃশ্যতা, জাতভাগ, হিংসা, ঘৃণা এবং বর্তমান সময়ে ধর্মের নামে সকল প্রকার পাপাচারের জন্মদাতা তিনি। তাই হিন্দুসমাজ বর্তমানে প্রায় পঙ্গু।”
এক রামে রক্ষে নেই তার উপর সুগ্রীব দোসর! ব্রাহ্মণ্যবাদকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আবির্ভাব হলেন রঘুনন্দন ভট্টাচার্য। ইনি আবার বল্লালসেনের চেয়ে এককাঠি উপরে। কে এই রঘুনন্দন ভট্টাচার্য? রাজা বল্লালসেনের কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন ও মানবসমাজকে চিতায় তুলে দিলেন এবং এরপর রঘুনন্দন সেই মানবসমাজের চিতায় অগ্নিসংযোগ করে ভস্ম করার দায়িত্ব হাতে তুলে নিলেন। নবদ্বীপে ভগ্ন-কুলীন ব্রাহ্মণের ঘরে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। সমাজরক্ষার ধুয়ো তুলে তিনি একটি গ্রন্থও রচনা করে ফেললেন। নাম ‘অষ্টাবিংশতিত্ত্ব স্মৃতি। উহাই হিন্দুসমাজে নতুন শাস্ত্র’ হইল। ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য বিস্তার করার জন্য তিনি ঘোষণা করলেন— “যুগে জঘন্যে দ্বিজাতি ব্রাহ্মণ শূদ্র এবহি”। অর্থাৎ- কলিযুগে মাত্র দুটি জাতি আছে একটি ব্রাহ্মণ ও অপরটি শূদ্র। রঘুনন্দন ক্ষুরধার ফতোয়া দিয়ে হিন্দুসমাজের ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সমাজকে বিলুপ্ত করলেন। তাঁর লেখনিতে বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাখ, পাল, সাহা, কুণ্ডু, নাপিত সহ সকল শ্রেণির হিন্দুমানুষ বল্লালসেনের গড়া জাতবিভাগে সবাই শূদ্র শ্রেণিতে ঘোষিত হল। রঘুনন্দন ব্রাহ্মণসমাজ যাতে সহজে শূদ্রদের শোষণ করতে পারে তাঁর লেখনীর মাধ্যমে নানাবিধ ব্যবস্থা করে দিলেন। ব্রাহ্মণ সমাজ রঘুনন্দনের নববিধান মুঠোয় পেয়ে শূদ্র জাতিকে শোষণের জন্য তৎপর হয়ে উঠল। শ্রাদ্ধ, বিবাহ, পঞ্চামৃত, সাধভক্ষণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, পুকুরখনন, গৃহপ্রবেশ, বিদেশযাত্রা, পুজো-পার্বন, তিথি, নক্ষত্রদোষ প্রভৃতি কাজে ব্রাহ্মণের খাজনা বা ভোলা চাই শূদ্রের কাছ থেকে। মৃত যজমান শ্মশানে চলেছে, সেখানেও ব্রাহ্মণের খাজনা আদায়। যজমান মৃত মাতা-পিতার বা পুত্র-কন্যার শোকে পাগল, ব্রাহ্মণ চোদ্দো পুরুষের পিণ্ডদানের ফর্দ করে শোকাতুর যজমানের শোকের অবসরে যজমানকে লুণ্ঠন ও শোষণ করে, রাস্তার ভিখারিতে পরিণত করে। কেননা ভিক্ষা করে হলেও ব্রাহ্মণদের আবদার পূরণ করতে হয় শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে। মৃতদের স্বর্গে বসবাসের জন্য কত রকমের ব্যবস্থা, কত রকমের ফন্দিফিকির। বিকল্পে মোটা অঙ্কের দক্ষিণা। যতটুকু তিল ততটুকু স্বর্ণ, জমি, সবৎস গাভী, ষোড়শ দান, পাত পেড়ে ভোজ সারা ইত্যাদি প্রাপ্তি। শোষণ করতে করতে লোভ এমন জায়গায় পৌঁছে গেছে যে ব্যক্তির পরমাত্মীয়ের মৃত্যু হওয়ার কারণে পেট ভরতি করে চব্যচোষ্য ভোজ করার মতো অমানবিক নিষ্ঠুর প্রথা চালু করা। বিয়ের আনন্দে ভোজ খাওয়া যেতেই পারে, সন্তান প্রথম ভাত খাচ্ছে সেই আনন্দেও ভোজ চলতেই পারে– তাই বলে কারোর প্রাণপ্রিয় আত্মীয়ের মৃত্যু হলে সেই আনন্দে ভোজ খাওয়া যায়? মৃত্যু কি আনন্দের বিষয়! কারোর আত্মীয়-বিয়োগ হলে কি সেই আনন্দে মিষ্টিমুখ করা যায়! মৃতদেহ সৎকার (দাহ বা কবর) করার পর আর কোনো কাজ থাকে না। তারপর যাঁর শোক সেই-ই বহন করে, আর কেউ নয়। বেদ তো তাই-ই বলে। শ্রাদ্ধ মানে শ্রদ্ধা জানানো, মস্তক মুণ্ডন করে গণ্ডায়পিণ্ডায় গেলানো নয়। আমরা যাঁরা শ্রাদ্ধের ভোজ খেতে যাই, তাঁরা কোন্ আনন্দে সেজেগুজে মৃতব্যক্তির বাড়ি গিয়ে মুখে অন্ন তুলি! নিজেকে অসভ্য, বর্বর, অমানবিক বলে মনে হয় না? না, মনে হয় না। মনে হয় না বলে আমরা শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে গিয়ে গিলতে গিলতে ত্রুটি খুঁজি, রান্নার ভালো-মন্দের চর্চা করি, আপ্যায়নের বিচার করি।
শূদ্রেরা মনে করেন ব্রাহ্মণরাই ব্রাহ্মণ-পুরোহিতরাই মানুষকে স্বর্গে পাঠানোর ঠিকা পেয়েছেন। মনে করেন ব্রাহ্মণের হাতেই মৃতব্যক্তির স্বর্গ ও নরক। ব্রাহ্মণের দাবি মেটালে স্বর্গ, না-মেটালে অবশ্যই নরকে ঠাঁই। শূদ্রের মাথায় ব্রাহ্মণের পা না-চড়ালে স্বর্গ কোথায়! ব্রাহ্মণের কাছে মাথা নত করলেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, সব পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। রঘুনন্দন এবার তাঁর ভেদনীতি আরও বিস্তার করলেন। বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাখ থেকে ডোম, মেথর পর্যন্ত, সকলকেই তিনি ব্রাহ্মণের দাস, শূদ্র বা গোলাম বলে ঘোষণা করলেন। তারপর তিনি শূদ্রদের মধ্যে কিছু ব্যক্তিকে সৎ বা অসৎ শূদ্র বলে ঘোষণা করলেন। রঘুনন্দনের প্রদত্ত উপাধি আবার কোনো কোনো শূদ্র খুব গর্বভরে গ্রহণ করেলেন। ভাবতে থাকলেন “আমি অন্য শূদ্রদের থেকে একটু ভালো, কারণ আমি কুলীন শূদ্র”। ব্রাহ্মণদের পদাঘাত নীরবে হজম করে শত শত শূদ্রগোষ্ঠী বা গোলামগোষ্ঠী অন্য শূদ্র বা গোলামদের উপর অত্যাচার শুরু করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করল না। তাঁরা ভুলে গেলেন যে– ‘আমরা সকলেই শূদ্ৰশ্রেণি তথাকথিত ব্রাহ্মণদের চোখে। ভুলে গেল বিয়ে, শ্রাদ্ধ, পুজো-পার্বন ইত্যাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে শূদ্রদের বসার আসন ব্রাহ্মণদের আসন থেকে সর্বদা আলাদা রাখা হয়।
অবমাননার এখানেই শেষ নয়। যেমন— শূদ্রের সামনে দেবতাকে ভোগ দেওয়া যাবে না। শূদ্রের সকারে কোনো ব্রাহ্মণ অংশগ্রহণ করতে পারবে না, অন্যথায় ব্রাহ্মণের ব্ৰহ্মত্ব নষ্ট হবে। ব্রাহ্মণদের হুঁকোয় শূদ্র শ্রেণির মানুষ তামাক পান করতে পারবে না। স্বামী বিবেকানন্দের বাড়িতে বৈঠকখানায় তাঁর বাবার বিভিন্ন জাতের জন্য আলাদা আলাদা হুঁকো সাজানো থাকত। পাছে জাত যায়, সেই কারণে কেউ কারোর হুঁকোয় মুখ দিতে পারত না। গল্প শোনা যায়, বিবেকানন্দ নাকি স্বয়ং সবকটি হুঁকোয় মুখ দিয়ে টেনে দেখেছিলেন কীভাবে জাত যায়। শ্মশানে শূদ্রের চিতা ভস্মের কাছাকাছি ব্রাহ্মণদের শবদাহ নৈব নৈব চ। শূদ্রের বেদে ও গায়ত্রী মন্ত্রে অধিকার নেই; শূদ্র ওম স্বধা বা স্বাহা প্রভৃতি বেদমন্ত্র উচ্চারণ করবে না। ব্রাহ্মণ শূদ্রের বাড়ির কোনো দেবতাকে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে পারবে না, কারণ শূদ্রের বাড়ির দেবদেবীও শূদ্র। কোনো পুরোহিত শালগ্রাম শিলা নিয়ে কোনো শূদ্রের বাড়ি যাবে না, গেলে সেই বিগ্রহকে প্রায়শ্চিত্ত করে ঘরে তুলতে হবে। শূদ্রের খাবার গ্রহণ করলে পাপ হয়। শূদ্রের বাড়ির পুজোর ভোগ শূদ্ৰান্ন, তাই কোনো অজুহাতেই এই খাবার গ্রহণ করা যাবে না। কোনো শূদ্র প্রতিমা বা ঠাকুরের মূর্তিকে স্পর্শ করবে না, অন্যথায় মূর্তিরূপ দেবতা অশুদ্ধ হয়ে যাবে, জাতিপাত হবে। আহা রঘুনন্দন বাবা, আপনি কত মহান!! আপনার সেই মানবজাতির অসন্মানের ধ্বজা আমরা বয়ে নিয়ে চলেছি পরম আনুগত্যে।
উচ্চ বর্ণবাদ-বিরোধী অনেক আন্দোলন এ ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে হয়েছে। এ বাংলাতেও কম হয়নি। কয়েকটি আমি আগেই উল্লেখ করেছি। সেইসব আন্দোলন প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যাচর্চায় অনালোচিত থেকে গেছে অনেক আন্দোলন। তাই বলে আন্দোলন থেমে থাকেনি। এমনই এক আন্দোলনের নাম মতুয়া আন্দোলন, পতিত আন্দোলন। মতুয়া আন্দোলনের স্রষ্টা হরিচাঁদ ঠাকুর এবং তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুর। হরিচাঁদ ঠাকুর ও গুরুচাঁদ ঠাকুর সমাজের পতিত নিচুতলার মানুষদের জন্যে ধর্মীয় মতাদর্শগত সংগ্রামের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যা পরবর্তীতে রাজনৈতিক সংগ্রামের পরিণত হয়। জাতি বর্ণ বিভক্ত হিন্দু সমাজ, অস্পৃশ্যতা এবং কঠোর ধর্মীয় অনুশাসনের বিরুদ্ধে নিবেদিত হয় মতুয়া ধর্ম আন্দোলন। সমাজের এই জাতপাতভিত্তিক বিপর্যয়ের জন্য হরিচাঁদ ব্রাহ্মণ্যধর্মকেই দায়ী করেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মই প্রধান নিয়ামক শক্তি। তাই বর্ণবিভক্ত সমাজ ব্রাহ্মণ্যধর্মকেই তিনি বেছে নেন। আক্রমণের লক্ষ্য হিসাবে। এর আগে তথাকথিত নিচুজাতের কোনো নিজস্ব কোনো ধর্ম ছিল না। হরিচাঁদই এইসব অন্ত্যজ ও অনুন্নত শ্রেণির মানুষদের জন্য নিজস্ব মতুয়া ধর্ম প্রচলন করেন। ধর্ম-কর্মে যাঁরা মাতোয়ারা তাঁরাই মতুয়া। হরিচাঁদ ‘হাতে কাম মুখে নাম’ এই বাণীর মাধ্যমে বলেন –নমঃশূদ্ররা কারও চেয়ে হীন বা নিচ নয়। কারও কাছে দীক্ষা নিও না বা তীর্থস্থানে যেও না। ঈশ্বর সাধনার জন্য ব্রাহ্মণদের প্রয়োজন নেই। বাংলার নিম্নবর্ণের নমঃশূদ্র, কাপালি, পৌ, নোয়ালা, মালো ও মুচিদের মধ্যে মতুয়া আন্দোলন জনপ্রিয়তা লাভ করে। অবশ্য এর প্রধান ভিত্তি হল নমঃশূদ্ররা। সংখ্যার দিক থেকে নমঃশূদ্ররা ছিল পূর্ববঙ্গের সবচেয়ে বড়ড়া জনগোষ্ঠী। হরিচাঁদের বার্তা কৃষিজীবী ও মৎস্য আহরণকারী নমঃশূদ্রদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছিল।
এই অসন্মানের ধ্বজা ড: ভীমরাও রামজি আম্বেদকর বয়ে নিতে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন, সোচ্চারেই। ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিলেন তিনি। বাবাসাহেব ভারতীয় ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ (অ্যারিস্ট), রাজনৈতিক নেতা, বৌদ্ধ আন্দোলনকারী, দার্শনিক, চিন্তাবিদ, নৃতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, বাগ্মী, বিশিষ্ট লেখক, অর্থনীতিবিদ, পণ্ডিত, সম্পাদক, রাষ্ট্রবিপ্লবী ও বৌদ্ধ পুনর্জাগরণবাদী এবং ভারতের দলিত আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা ছিলেন। তিনি গরিব ‘মহর’ পরিবারে (তখন অস্পৃশ্য জাতি হিসাবে গণ্য হত) জন্মগ্রহণ করেন। আম্বেদকর সারাটা জীবন সামাজিক বৈষম্যতার, ‘চতুর্বর্ণ পদ্ধতি’ হিন্দু সমাজের চারটি বর্ণ এবং ভারতবর্ষের অস্পৃশ্য প্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেছেন। অস্পৃশ্য’ আম্বেদকরও জাতিবৈষম্যের সম্মুখীন হয়েছিলেন। অন্যান্য অস্পশ্যদের সঙ্গে আম্বেদকরও বিদ্যালয়ে যেতেন, কিন্তু তাঁদের আলাদা করে বসতে দেওয়া হত ক্লাসঘরে এবং শিক্ষকগণ দ্বারা অমনোযোগী ও অসহায়ক ছিলেন। তাঁদের শিক্ষাকক্ষের ভিতরে বসার অনুমতি ছিল না, এমনকি তাঁদের যদি তৃষ্ণা পেত উচ্চশ্রেণির কোনো একজন উঁচু থেকে সেই জল ঢেলে পান করাত। কারণ নিম্নশ্রেণিদের জলস্পর্শ করার কোনো অনুমতি ছিল না। পরবর্তী সময়ে আম্বেদকরের প্রসিদ্ধি এবং অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের জনপ্রিয় সমর্থনের কারণে, তাঁকে ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে লন্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে (Second Round Table Conference) আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধি অস্পৃশ্যদের জন্য গঠিত পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর প্রচণ্ডভাবে বিরোধিতা করেন। যদিও তিনি অন্য সকল সংখ্যালঘুদের যেমন মুসলমানদের ও শিখদের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী (Separate Electorate) বিনা দ্বিধায় মেনে নেন এই বলে যে, তিনি অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের গঠনকৃত নির্বাচকমণ্ডলী হিন্দুসমাজকে ভবিষ্যতে বিভক্ত এবং উচ্চশ্রেণির ক্ষমতা কমিয়ে দিতে পারে। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে যখন ব্রিটিশরা আম্বেদকরের সঙ্গে একমত হন এবং পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীদের ঘোষণা করেন, তখন মহাত্মা গান্ধি পুনের এরোদা কেন্দ্রীয় কারাগারে (Yerwada central jail) শুধুমাত্র অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর বিরুদ্ধে উপবাস শুরু করেন। গান্ধির এই উপবাস (fast) ভারতজুড়ে বেসামরিকদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের উদ্দীপনা জোগায় এবং ধর্মীয় গোঁড়াবাদী নেতারা (Orthodox Politicians), কংগ্রেস নেতারা কর্মীদের মধ্যে মদনমোহন মালব্য ও পালঙ্কর বালো ও তাঁর সমর্থকরা আম্বেদকরের সঙ্গে এরাভাদে (Yeravada) যৌথ বৈঠক করেন। গান্ধিবাদীদের প্রবল চাপের মুখে (Massive coercion) এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিশোধ (Communal reprisal) ও অস্পৃশ্য সম্প্রদায়কে নির্মূলীকরণের আশংকায় আম্বেদকর পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী বাতিল করতে সম্মত হন। এই চুক্তির পরে গান্ধি উপবাস পরিত্যাগ করেন। ইতিহাসে এটি পুনে চুক্তি নামে পরিচিত। চুক্তির ফলশ্রুতিতে, আম্বেদকর পৃথক নির্বাচকমন্ডলী গঠনের দাবি ছেড়ে দেন, যা আম্বেদকর গান্ধির সঙ্গে বৈঠকের আগে ব্রিটিশ সাম্প্রদায়িক কর্তৃক শর্ত সাপেক্ষে মঞ্জুর করে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ হন। একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন অস্পৃশ্যদের জন্য সংরক্ষিত হয়। এই চুক্তিতে যাকে বলা হয় অস্পৃশ্য সম্প্রদায় (Depressed class)।
বাবা সাহেবের প্রথম স্ত্রী রামাবাই দীর্ঘ অসুস্থতার পরে মৃত্যুবরণ করেন। অসুস্থ অবস্থায় তাঁর স্ত্রী রামাবাইয়ের পান্দরপুর তীর্থে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। কিন্তু আম্বেদকর তাঁকে যেতে দিতে অস্বীকৃতি জানান এই বলে যে, তিনি তাঁকে বরং একটি নতুন পান্দরপুর বানিয়ে দিবেন হিন্দু পান্দরপুরের পরিবর্তে– যেটা কিনা তাঁদের অস্পৃশ্য বলে গণ্য করে। ১৩ অক্টোবর নাসিকের কাছে ঈওলার বৈঠকে বক্তব্যে আম্বেদকর তাঁর ভিন্ন ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার অভিপ্রায় ঘোষণা করেন এবং তাঁর অনুগতদেরও হিন্দুধর্ম ত্যাগে প্রণোদিত করেন। নিউইয়র্কে লিখিত গবেষণালব্ধ উপাত্তের ভিত্তিতে একই বছর তিনি তাঁর বই ‘The Annihilation of Cast’ প্রকাশ করেন। ব্যাপক জনপ্রিয় সাফল্যে অর্জনের পর, আম্বেদকর গোঁড়াবাদী ধর্মীয় নেতাদের এবং নিম্ন সাধারণের জন্য অস্পৃশ্য, বর্ণপ্রথার তীব্র সমালোচনা করেন। কংগ্রেস ও গান্ধি অস্পৃশ্যদের প্রতি যা করেছিল, আম্বেদকর কপটতার সহিত তীব্রভাবে গান্ধী ও কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন। তাঁর কাজের মধ্যে ‘who were Shudras?’ প্রবন্ধে বর্ণনা করতে চেষ্টা করেন। শূদ্র বর্ণ গঠিত হয় অর্থাৎ পুরোহিত তন্ত্রের হিন্দু বর্ণ প্রথার (Hierarchy of Hindu Caste System) নিম্নবর্ণ গঠনের উপর আলোকপাত করেন। তিনি এও উল্লেখ করেন শূদ্র কীভাবে অস্পৃশ্য থেকে আলাদা। তিনি সারা ভারতের সিডিউল কাস্টেস ফেডারেশনে তাঁর রাজনৈতিক দল বদলে তদারকি করেন, যদিও তা ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতের সংবিধান পরিষদের নির্বাচনে ভালো করেনি। পরিশিষ্ট লিখতে গিয়ে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে আম্বেদকর হিন্দুবাদকে কর্কশ ভাষায় সমালোচনা করেন তাঁর “The untouchable : a thesis on the origins of untouchability’-60 901– “The Hindu Civilisation…. is a diabolical contrivance to suppress and enslave humanity. Its proper name would be infamy. What else can be said of a civilisation which has produced a mass of people…. who are treated as an entity beyond human intercourse and whose mere touch is enough to cause pollution?” অর্থাৎ “হিন্দু সভ্যতা… হচ্ছে মানবতাকে দমন এবং পরাভূত করতে একটি পৈশাচিক কৌশল। এর প্রকৃত নাম হবে সামাজিক কুখ্যাতি। কাকে সভ্যতা বলে ডাকা যায়, যার একগাদা মানুষ…., যাদের সত্ত্বা মানব সম্পর্কের নীচে গণ্য হয় ও শুধু যাদের ছোঁয়া দূষণের জন্য যথেষ্ট?”
দলিত বৌদ্ধ আন্দোলন বা নববৌদ্ধ আন্দোলন হল বিশ শতাব্দীতে সিংহলী বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের সহায়তায় ভারতের নিম্নজাতিদের নিয়ে গড়ে ওঠা একটি বৌদ্ধ নবজাগরণ। ভারতের নিম্নজাতি আন্দোলনের পুরোধা ভীমরাও আম্বেদকর বর্ণাশ্রম ভিত্তিক ব্রাহ্মণ হিন্দুসমাজের নিন্দাপূর্বক সমস্ত নিম্নজাতি, অর্থাৎ শূদ্রাদি নিম্নবর্ণীয় ব্যক্তিদেরকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হতে আহ্বান জানান এবং এর ফলে এই আন্দোলন বিশেষ তাৎপর্য লাভ করে।
১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে ইয়েবেলা সম্মেলনে বাবাসাহেব ভীমরাও আম্বেদকর ঘোষণা করেন যে, তিনি কিছুতেই একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী হিসাবে মৃত্যুবরণ করবেন না। কারণ হিন্দুধর্ম বর্ণভিত্তিক সমাজব্যবস্থার মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে বিভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। এর প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ আম্বেদকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং প্রত্যেকেই তাঁদের ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার আহ্বান জানান। এরপর বিভিন্ন নিম্নজাতিদের ধর্মান্তরিত হওয়ার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিকগুলি দিয়ে আলোচনা করেন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ২২ মে লখনউতে একটি ‘সর্বধর্ম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জগজীবন রাম সহ বহু বিশিষ্ট দলিত নেতৃবর্গ উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। যদিও বাবাসাহেব আম্বেদকর এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে পারেননি। তবে এই সম্মেলনে ইসলাম, খ্রিস্টধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম সহ বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিরা তাঁদের ধর্মের গুণাবলি দলিত নেতাদের সামনে ব্যাখ্যা করেন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুন ভিক্ষু লোকনাথ বাবাসাহেব আম্বেদকরের দাদরের বাসভবনে গিয়ে সাক্ষাৎ করেন এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেন। পরে গণমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বৌদ্ধভিক্ষু লোকনাথ ঘোষণা করেন –“আম্বেদকর বৌদ্ধধর্মের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন এবং সমগ্র দলিত সম্প্রদায়কে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।” ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে লোকনাথ তাঁর সিংহলে অবস্থিত ছাপাখানা থেকে ভারতের নিপীড়িত এবং দলিত সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করেন, যাতে লেখা হয় –বৌদ্ধধর্ম আপনাদের মুক্তি এনে দেবে।
এত কিছু করেও কি বাবা সাহেব সমাজকে বদলাতে পেরেছে? না, পারেনি। সমাজ যেখানে ছিল সেখানেই আছে। কারণ বাবা সাহেবের বার্তা দেশের সর্বত্র পৌঁছায়নি। কারণ অনুসরণকারীদের সদিচ্ছার অভাব। জাতপাতকে সামনে রেখে ভারতীয় রাজনীতিকদের নোংরা রাজনীতি আজও সমান বহমান।
জাতপাতের বিভাজন সামাজিকভাবে এমন নির্যাতনের রূপ নিয়েছিল যে, সমাজে নিম্নবর্গের মানুষদের ঠেকাটাই দায় হয়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষে এই বিভাজনের মধ্য দিয়ে বিস্তৃতি ঘটে বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মের। কিন্তু জাতপাতের সংকট ভারত-বাংলাদেশ থেকে আজও যায়নি। এখনও জাতপাতের তাম্রলিপিতে দলিত সম্প্রদায়েরা রয়ে গেছে। মহাত্মা গান্ধি দলিতদের মেথর, সুইপার না বলে ‘হরিজন’ বলার বাণী দিয়ে গেছেন। কিন্তু তাঁদের সমাজ ও সামাজিকতার মূল সমাজের সঙ্গে যুক্ত করেনি। অর্থাৎ এক একজন শাসক জাতি বিভাজন করলেও তাঁকে টিকিয়ে রেখেছেন ব্রাহ্মণসমাজ। মহাত্মা গান্ধির হরিজন’ তার একটি প্রকাশ মাত্র।
গো-বলয়ে নিম্নজাতিদের ‘দলিত’ বলা হয়ে থাকে। প্রকৃতভাবে বিচার করলে দেখা যাবে সাংবিধানিকভাবে যাদেরকে বাবাসাহেব নাম দিয়েছেন তফসিলি জাতি বা অনুসূচিত জাতি, তাঁদেরকেই গো-বলয়ে দলিত বলা হয়। এখন প্রশ্ন কেন তাঁদের দলিত বলা হয়? তাঁদের তো সাংবিধানিক নাম আছে, তবুও তাঁদের প্রতি এই ‘দলিত’ শব্দের প্রয়োগ কেন? বাবাসাহেবের কোনো লেখা বা ভাষণে আমরা কি কোথাও দলিত’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন? না, পাইনি। ভারতের সংবিধান রচিত হওয়ার পূর্বে যাঁদের অস্পৃশ্য (untouchable) বলে গণ্য করা হত পতিত বলে মনে করা হত, তাঁদের সাংবিধানিকভাবে দু-ভাগে ভাগ করা করা হয়েছে– (১) তফসিলি জনজাতি ও (২) তফসিলি উপজাতি। কারা কোন্ জাতির মধ্যে পড়ে তার বিস্তারিত তালিকা তৈরি করা আছে। তবে অনেক পরে আরও একটা তালিকা তৈরি করা হয়েছে, তার নাম দেওয়া হয়েছে ওবিসি (other Backward class/OBC)। বাবাসাহেব এঁদের সবাইকেই অস্পৃশ্য বলে চিহ্নিত করেছেন, দলিত বলেননি। তবে গো-বলয়ে এই শ্রেণির জনগোষ্ঠীকে দলিত বললেও বাংলায় কিন্তু নমঃশূদ্র বলা হয়।
তাহলে আমরা দেখে নেব ‘দলিত’ শব্দের উৎপত্তি কোথা থেকে? ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কৌশল হল তাঁরা কখনো সামনে থাকবে না। বরং হাতে থাকবে রিমোর্ট। যা ঘটবে, তা আড়াল থেকে পরিচালিত করা হবে। তাঁরা আমাদের আপন ভাই-জাতি-গোষ্ঠীকে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়িয়ে দেবে। আর এই লড়াইয়ে যে পক্ষেরই জয় হোক না-কেন, সে জয় তাঁর নয়। সেই জয় হবে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের। তেমনিভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা কৌশল করে বাবাসাহেবের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিপক্ষ তৈরি করার জন্য মাধ্যমিক লেভেল থেকে মেধাবী জগজীবন রামকে সমস্তরকম সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে লালনপালন করে সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলে। আর ধীরে ধীরে জগজীবন রামকে বাবাসাহেবের প্রতিপক্ষ হিসাবে খাড়া করে। কংগ্রেস এই জগজীবন রামের মাধ্যমে দলিত বা দলিত নেতা শব্দের বিস্তার ঘটাতে শুরু করে। জগজীবন রাম যে সংগঠন তৈরি করেছিলেন, তার নাম ‘দলিত বর্গ সংঘ’। আর বাবাসাহেব তাঁর সংগঠনের নাম দিয়েছিলেন Scheduled Caste Federation। বাবাসাহেব মহাপরিনির্বাণের পূর্বে যে RPI (Republican Party of India)-র নির্মাণের পরিকল্পনা করেছিলেন, পরবর্তীতে কংগ্রেস সেই আরপিআই-এর মাধ্যমে দলিত’ শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার শুরু করে।
‘দলিত’ শব্দটি কী খুব গর্বের? বহুজন বা বা মূলনিবাসী বলেও অনেকে চিহ্নিত করেন। মূলনিবাসী শব্দেও অনেকের এলার্জি আছে। সংগঠনের নামে ‘বহুজন’ লেখা থাকবে, আবার ‘দলিত’ ‘দলিত’ বলে গলা ফাটাব –সেটা কি ভাবনা ও কর্মের মধ্যে বিশাল অন্তর সৃষ্টি করছে না? কিন্তু আমরা নিশ্চয় SC, ST, OBC ও converted minority-দের মিলন চাই বহজনবাদী ভাবনায়। আর দলিত বলতে যেখানে শুধু সিডিউল কাস্টদেরই বোঝানো হয়, তাহলে সাংবিধানিক শব্দ তফসিলি জাতি বা অনুসূচিত জাতি শব্দগুলোকে ব্যবহার করব না? ব্যবহার হয় না তা নয়, তবে সেগুলি সরকারি কাগজপত্রে।
ভারতে প্রথম জনগণনা হয় ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে। সেখানে নমঃশূদ্রদের কোনো উল্লেখ ছিল না। তখন তাদের বলা হত ‘চণ্ডাল’ বা ‘চোঙ’। অবশ্য ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের জনগণনায় অবমাননাকর ‘চণ্ডাল’ নামের অবলুপ্তি ঘটে। জনগণনায় ‘চণ্ডাল’ নামের অপসারণ ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু অস্পৃশ্যতা আজও ঘোচেনি। চণ্ডাল একটি বল-বীর্য সমন্বিত অর্থ দ্যোতক শব্দ। চণ্ডের সঙ্গে জাতিসূচক ‘আল’ প্রত্যয় যুক্ত হলে চণ্ডাল হয়। এমনিভাবে লাঙ্গল, জোঙ্গাল, জঙ্গল, ডাঙ্গাল, বহাল, খেড়ওয়াল, সাঁওতাল, বঙ্গাল প্রভৃতি আদি অস্ট্রাল শব্দগুলির ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ করলেই ‘চণ্ডাল’ শব্দের গুণগত এবং অর্থগত অভিব্যক্তিটি যথার্থ প্রতিভাত হয়ে উঠবে। ঋকের অনেকগুলি শ্লোকের রচয়িতা বিশ্বামিত্র ছিলেন চণ্ডাল। গুহক চণ্ডাল, রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনি অনন্যতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। জাতক কাহিনিতে বোধিসত্ত্বকে সতোর প্রতীক হিসেবে ‘চণ্ডাল’ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে বহুবার। কার্যসিদ্ধির জন্য সুদাস, মনু, অগ্নী, বরুণ। প্রভৃতি দাস বা অসুর নেতাদেরও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত বৈদিক সাহিত্যে। অর্থাৎ রক্ষস (পরবর্তীকালে রাক্ষস বলা হয়েছে), অসুর, নাগ, চণ্ডাল শব্দগুলি কোনোভাবেই ঋণাত্মক নয়— বরং গুণবাচক এবং ঋনাত্মক। অন্যদিকে ‘নমঃশূদ্র’ শব্দটি একেবারেই অর্বাচীন ব্রিটিশ আমলের আরোপিত হীনাত্মক শব্দ। শূদ্র’ শব্দের ‘নমঃ’ জুড়ে দিলেই নমস্য হয়? হয়েছে কি?
১৯১১ খ্রিস্টাব্দে সেন্সাসে বাঙলার জাতিগুলির মধ্যে নাম পরিবর্তনের একটা হিড়িক তৈরি করা হয়েছিল। তথাকথিত ছোটজাতগুলিকে হিন্দুভুক্ত করার জন্য বাংলার তৎকালীন দিকগজ পণ্ডিতদের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। ‘জাতির উন্নয়ন’ নামক গালভরা নামকরণের আড়ালে তাঁরা বিজ্ঞাপন জারি করেছিলেন। প্রায় চল্লিশজন নামকরা মহাপণ্ডিত এই বিজ্ঞাপনে সই করে লিখেছিলেন –“The caste called Namasudra is Brahmin by origin beging descended from the great Brahmin, Kashypa and not ‘chandal’।” শুধু চণ্ডাল নয়, এই হিড়িকে সামিল হয়েছিল বাংলা, বিহার ও আসামের তথাকথিত ছোটোজাতেরা। আবেদনপত্রের ওজন ছিল দেড় মন। চণ্ডালেরা চেয়েছিল নমঃ ব্রাহ্মণ নাম, কোচরা চেয়েছিল ক্ষত্রিয়, বৈদ্যরা চেয়েছিল ব্রাহ্মণ, কাপালিরা চেয়েছিল বৈশ্যকাপালি, বাগদিরা চেয়েছিল ব্যগ্রক্ষত্রিয়, হাঁড়িরা চেয়েছিল ক্ষত্রিয়, সুবর্ণ বণিকেরা চেয়েছিল বৈশ্য আর পোদরা চেয়েছিল পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়। বিহারের ভূমিহারেরা হল ব্রাহ্মণ। কায়স্থরা প্রথমে শূদ্র পরে ক্ষত্রিয়। দুসাদেরা দাবি করেছিল ক্ষত্রিয়ত্বের। এর আসল কারণ ছিল আইন সভায় সংখ্যা অনুপাতে প্রতিনিধিত্ব করা। বিংশ শতকের শেষ দশকে আগা খাঁ ভাইয়েরা যখন সঠিকভাবে লোক গণনার জন্য সরকারকে চাপ দিচ্ছিলেন এবং বারবার প্রমাণ দাখিল করছিলেন যে, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল, সাঁওতালরা কেউই হিন্দু নয়। যাই হোক ‘জাতির উন্নয়ন’ নামে তৎকালীন ছোটোজাতগুলির মধ্যে হিন্দুকরণের হিড়িক পড়ে যায়। ব্রাহ্মণের আইনসভায় যাওয়ার প্রতিনিধি সংখ্যা বাড়ে। কিন্তু জাতিগুলি সিডিউল্ড তালিকা ভুক্ত হয়ে ব্রাহ্মণের স্থায়ী দাসে পরিণত হয়ে যায়। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের সেনসাসে স্বাধীন বোধি চিত্তসম্পন্ন একটি প্ৰাগ বৈদিক জাতি শূদ্ৰত্বে উন্নীত হয়।
নমো বা নম নামের বিসর্গীকরণ (ঃ) হয়েছে নমঃশূদ্র নাম হওয়ার পরে। সেনসাসে নমোরা চণ্ডাল থেকে নমঃশূদ্র হয়েছে ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে। নমো নেতারা ‘নমো’ নামটি উদ্ধার করতে অনেক সংগ্রাম চালিয়েছেন। কিন্তু সর্বপ্রথম দলবদ্ধভাবে আন্দোলন হয় ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম লোকগণনাতে। বাংলায় নমোরা ‘চণ্ডাল’ নামে চিহ্নিত হয়েছেন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের আগমনের পর, শুধুমাত্র ‘নিন্দাসূচক বাক্য হিসাবেই। কারণ সম্পদ সৃষ্টিকারী এই সুবিশাল জনগোষ্ঠীর তথাকথিত কোনো ধর্ম ছিল না।
তথাকথিত ‘ধর্ম’ ছিল না, তাই কোনো তথাকথিত ধর্ম মানার দায়ও এই গোষ্ঠীর ছিল না। তাই ব্রাহ্মণরাই তো বটেই, এমনকি বৌদ্ধরাও নিজ ধর্মে টানতে অসমর্থ হয়ে এই জাতিকে ‘চণ্ডাল’ নামে ভূষিত করেছিলেন! অথচ চণ্ডাল একটি আর্যভাষী জনগোষ্ঠী, যারা উত্তর-পশ্চিম ভারতের লোক এবং ব্রাহ্মণ্যসমাজ কর্তৃক নিন্দিত। বাংলায় ব্রাহ্মণ্য বা হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত ব্রাহ্মণ বা অন্যান্যরা যে নমো নরগোষ্ঠীর লোক সে-কথা নৃতাত্ত্বিক পরিমিতিতেও পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার বলেছেন, ভারতীয়রা যে হিন্দু তাঁরা জানতেই পারতেন না, যদি গ্রিকরা সমুদ্রপথে পূর্বদিক থেকে আক্রমণ করতেন। তখন তাঁদের সিন্ধুনদী অতিক্রম করতে হত না, আর গ্রিক উচ্চারণে ‘সিন্ধু’ নদী ‘হিন্দু’ হত না। ভারতীয়রা হিন্দু হওয়ার পরে সবচেয়ে বড়ড়া হিন্দু সেজেছেন ব্রাহ্মণরা (আমার অন্য একটি প্রবন্ধে জনৈক ব্রাহ্মণ-পাঠক সরাসরিই বলেছিলেন ব্রাহ্মণরাই সনাতন ধর্মকে টিকিয়ে রেখেছে’)— অবশ্যই নিজেদের স্বার্থে এবং গণসমর্থন পাওয়ার লক্ষ্যেই। যে লক্ষ্যে তাঁরা ১০০ ভাগ সফল, একথা বলাই বাহুল্য। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র সৃষ্টির জন্য বল্লালসেন যখন বাংলায় বৌদ্ধদের কচুকাটা করেন এবং বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে জাতপাত সৃষ্টি করেন, তখনও নমোরা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেননি। রাষ্ট্রশক্তির বহির্ভূত হয়েও এই জাতি ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অন্যায়ের বিরুদ্ধে বারবার প্রতিরোধ সংগ্রাম করেছিলেন। পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতে সেইসব আর্য-অনার্যদের যুদ্ধ বা সংগ্রামের কাহিনিই স্বর্ণাক্ষরে বর্ণিত আছে। বলা হয়, আমীষভোজী এই নমোগোষ্ঠী জৈবিক জীবনযাপনে যেমন বৌদ্ধ হতে পারেন না, তেমন মানবিক কারণে ব্রাহ্মণ হওয়াও সম্ভব নয়। তাহলে কীভাবে নমোদের নামের সঙ্গে শূদর যোগ করে তাঁদেরকে হিন্দু করা হল? ‘আত্মসমর্পণ না-করা এই নমোগোষ্ঠীকে ‘চণ্ডাল নামে নথিভূক্ত করে রেখেছিল ব্রাহ্মণ্যবাদীরা।
বড়োলাট ওয়াভেল সকাশে উপস্থিত হয়ে ভারতীয় হিন্দু অস্পৃশ্যদের কংগ্রেসী নেতা বাবু জগজীবন রাম আবেদন জানান– ইংরেজদের উচিত আরও দশ বছর ভারতে তাঁদের দখল কায়েম রাখা। কারণ ইংরেজদের অবর্তমানে বর্ণহিন্দুরা নীচুজাতের মানুষদের উপর নিপীড়ন আর অত্যাচার আরও বাড়িয়ে দেবে (ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশবিভাগ– লাডলীমোহন রায়চৌধুরী, পৃষ্ঠা ৯)। বাবু জগজীবন রামের এই বয়ান থেকে আন্দাজ করা যায়, মহাত্মা গান্ধির হরিজনদের দুর্গতি ছিল কতটা অসহনীয় ছিল। সেই কারণেই বাবু জগজীবনের কাছে কংগ্রেসী শাসনের অপেক্ষা পরাধীনতা তথা ইংরেজদের ন্যায় বিচার অধিকতর গ্রহণীয় ছিল। অস্পৃশ্য সমাজের নেতা আম্বেদকর গান্ধি প্রদত্ত ‘হরিজন’ অভিধাকে অভিহিত করেছিলেন ‘রাজনৈতিক অনুকম্পা’ বলে। আজও অস্পশ্যতা আইনত দণ্ডনীয় হওয়া সত্ত্বেও ‘গণতান্ত্রিক’ ও ‘সেকুলার’ ভারতে নির্বাচনের মরশুমে দেখা যায় রাজনৈতিক অনুকম্পা’-র মহোৎসব। স্বাধীনোত্তর ‘সেকুলার’ ভারতে মন্দির অপবিত্র করার অছিলায় ‘হরিজন’ বধ তো নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। প্রকৃত ধর্মহীন বা সেকুলার মতাদর্শ আমাদের সমাজ প্রগতির শর্ত সৃষ্টি করতে পারে, কিন্তু রাজনীতির দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা হিন্দুত্ববাদী সংস্কৃতির বিলোপসাধন করবেন না। কারণ এই ব্যবস্থাই তাঁদের পুষ্টিসাধন করে। গান্ধিজি বললেন– “অস্পৃশ্যতা বিলুপ্ত হবেই, কারণ হিন্দুধর্ম বাঁচবে, আর যদি অস্পৃশ্যতা দূর না-হয় তাহলে হিন্দুধর্ম অবলুপ্ত হবে।” বাবা সাহেবও একই সুরে বলেছিলেন –“হিন্দুসমাজ যদি জাতব্যবস্থা মুক্ত না-হয়, তবে তাঁরা নিজেদের রক্ষা করার শক্তি অর্জন করতে পারবে না।” ডঃ আম্বেদকর আরও বলেছেন –“আজ প্রয়োজন সমস্ত নির্যাতিত ও বঞ্চিত শ্রেণির মানুষের একত্রিত হয়ে ভারতের মাটি থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদের মূল উৎপাটন করে ফেলা। অন্যথায় তাঁরা মানুষের অধিকার নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না।” একুশ শতকের ভারতে সাংবিধানিক বিধিনিষেধ সত্ত্বেও সমাজজীবনে আজও কিন্তু অস্পৃশ্যতার ঘৃণা খর্ব করা যায়নি। হিন্দুধর্মের অচলায়তন পূর্ববৎ স্থানুই রয়ে গেছে।
১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে সংবিধানে বিবৃত ১৭ নম্বর ধারা বলে সারা ভারতে অস্পৃশ্যতার বিলোপসাধন করা হয়। কিন্তু হিন্দুত্বের জগদ্দল পাথরে কোনো আঁচড় পড়ল না তাতে। ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট, চুনি কোটালকে মনে পড়ছে? পশ্চিম মেদিনীপুরের দলিত আদিবাসী লোধা শবর সমাজের মেয়ে চুনি। তিনিই শবরদের প্রথম গ্রাজুয়েট। নিজ সমাজকে অশিক্ষার অন্ধকার থেকে টেনে বের করে আনার ব্রত নিয়ে উচ্চতর শিক্ষা অর্জনের জন্য ভর্তি হয়েছিলেন মেদিনীপুরের বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু তার স্বপ্ন পূরণ হতে দেয়নি জাতপাতের প্রবর্তক সমাজপতিরা। ইউনিভার্সিটিতে তাঁকে এই সমাজপতিদের কঠিন বর্ণবৈষম্যের শিকার হতে হয়। একজন শিক্ষিত সমাজ সচেতনার প্রতি শুধু আদিবাসী হওয়ার কারণে দেশের সমাজপতিদের এই বৈষম্যমূলক আচরণ, অসহযোগিতা তিনি মেনে নিতে পারেননি। ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজব্যবস্থার প্রতি ধিক্কারে, ক্ষোধে, দুঃখে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন। স্বাধীনতা দিবসের পরের দিনে চুনি কোটাল জীবন দিয়ে প্রমাণ করে গেল এদেশের দলিত আদিবাসী মূলনিবাসীদের বর্ণবৈষম্যের নিপীড়ন থেকে আজও মুক্তি দেয়নি ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ। ব্রাহ্মণ্যবাদের বলি হলেন অন্ত্যজ চুনি কোটাল। যাঁদের জন্য যাঁদের প্ররোচনায় চুনি কোটাল আত্মহত্যা করলেন তাঁদের কোনো শাস্তি হয়েছে বলে আমি শুনিনি।
চুনি কোটালের সত্যিকারের সমস্যা শুরু হয় যখন তিনি স্থানীয় বিদ্যাসাগর মাস্টার্স কোর্সে (এমএসসি) যোগ দেন। এখানে তিনি ধারাবাহিকভাবে তাঁর উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ অধ্যাপক ফাল্গুনী ও অন্যান্যরা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসকদের দ্বারা বৈষম্যমূলক আচরণ এবং প্রতিনিয়ত অপমানিত হতে থাকেন, যাঁরা তাঁকে প্রয়োজনীয় পাস গ্রেড দিতে অস্বীকৃতি জানায়। যদিও চুনি কোটাল তাঁর সকল ধরনের মানদণ্ড পূর্ণ করেছিলেন। অপমানিত ও হতাশ চুনি ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট মাত্র ২৭ বছর বয়সে আত্মহত্যা করেন। শুভব্রত সুর ‘হার মানা হার’ উপন্যাসে চুনি কোটাল আজও বেঁচে আছে। তার বাইরে সবাই ভুলে গেছে। তবে মহাশ্বেতা দেবীর ‘বিয়াধথান্দা’ (১৮৮৪) ও ‘দি বুক অব দি হান্টার’ গ্রন্থে চুনি কোটালের আত্মহত্যার বিষয়টি আলোকপাত করেছেন।
অনেক নামই উল্লেখ করা যায়। কিন্তু এত জায়গা কোথা থেকে দেব? পায়েলের কথা বলি। ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে হাসপাতাল ক্যাম্পাসের মধ্যেই আত্মহত্যা করেন মুসলমান উপজাতি সম্প্রদায় থেকে পড়তে আসা বিওয়াইএল নায়ার হাসপাতালের রেসিডেন্ট চিকিৎসক পায়েল তদভি। নিজের হাসপাতালেই জাতিবিদ্বেষমূলক অপমান ও হেনস্থার শিকার হতে হয় ডাক্তার পায়েল তদভিকে। মাসের পর মাস হেনস্থা চালাতে থাকে তিন হিন্দু উচ্চবর্ণ সিনিয়র চিকিৎসক হেমা আহুজা, ভক্তি মেহর ও অঙ্কিতা খাণ্ডেলওয়াল। এই তিন সহকর্মীর দ্বারা একদিকে যেমন কর্মক্ষেত্রে ক্রমাগত অত্যাচারের শিকার হন পায়েল, অন্যদিকে হস্টেলেও তাঁকে নানাভাবে হেনস্থা করতে থাকে এই তিনজন। জাতিবিদ্বেষমূলক মন্তব্য, উপজাতি পরিচয় নিয়ে হেনস্থা ও হস্টেলের ভিতর রেগিং হয়ে ওঠে নিত্যদিনের ঘটনা। পাশাপাশি চলে সামাজিক মাধ্যমে নীতিপুলিশি। কর্মক্ষেত্রে রোগীদের সামনেই পায়েলকে নানাভাবে হেনস্থা করতে থাকে এই সিনিয়র চিকিৎসকরা। অপারেশন করতে বাধা দেওয়া হয় পায়েলকে, ঢোকা বন্ধ করে দেওয়া হয় অপারেশন থিয়েটারে। ডিন ও বিভাগীয় প্রধানের কাছে তাঁর নামে অভিযোগ করা হবে বলে শাসানো হতে থাকে পায়েলকে। অত্যাচারী এই ডাক্তারদের মধ্যে দুজনের সঙ্গে এক ঘরে থাকতে বাধ্য করা হয় তাঁকে, সেখানেও সমান ভাবে চলতে থাকে অত্যাচার ও হেনস্থা। হস্টেলের ঘরের মেঝেতে তোষক পেতে শুতে বাধ্য করা হয় পায়েলকে। বাথরুম পায়খানা থেকে এসে পায়েলের সেই তোষককে পাপোস হিসেবে ব্যবহার করত হেমা ও ভক্তি। হেনস্থা চলে হোয়্যাটস্অ্যাপ গ্রুপেও, তাঁর উপজাতি পরিচয় নিয়ে সেখানেও ক্রমাগত আক্রমণ চালাতে থাকে ওই তিন উচ্চবর্ণের চিকিৎসক। এরপর হস্টেল ছেড়ে হাসপাতালে রাত্রি কাটাতে বাধ্য হন পায়েল। সিনিয়র চিকিৎসকদের থেকে শুনতে হয়, “আমরা ওদের পড়াশোনা করতে দেব না। ওদের সঙ্গে এভাবেই ব্যবহার করা হবে। এরা নীচুজাতের লোক, এদের সঙ্গে এইভাবেই ব্যবহার করা উচিত।”
পায়েলের আত্মহত্যার পর তাঁর মায়ের অভিযোগের ভিত্তিতে ও বিভিন্ন দলিত ও আদিবাসী সংগঠনের চাপে বিশেষ কমিটি গঠন করতে বাধ্য হয় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। কমিটির রিপোর্টে উঠে আসে পায়েলের উপর দিনের পর দিন চলা অত্যাচারের কথা। অভিযুক্ত তিন ডাক্তারকে গ্রেফতার করে পুলিস। হেমা আহুজা, ভক্তি মেহর ও অঙ্কিতা খাণ্ডেলওয়ালের বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনা, জাতিবিদ্বেষ বিরোধী আইন, অ্যান্টি রেগিং অ্যাক্ট, আইটি অ্যাক্ট-এ অভিযোগ দায়ের হয়েছে।
পায়েলের মৃত্যুকে শুধুমাত্র আত্মহত্যা বা ব্যক্তির সিদ্ধান্ত হিসাবে দেখা একটি অপরাধ। পায়েলের মৃত্যুর জন্য দায়ী আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রাতিষ্ঠানিক জাতিবিদ্বেষ। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি, হায়দ্রাবাদ কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আম্বেদকারাইট ছাত্র রোহিত ভেমুলার প্রাতিষ্ঠানিক হত্যা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রগুলিতে কীভাবে বিদ্বেষমূলক আচরণের শিকার হতে হয় সমাজের নিম্নবর্ণ থেকে পড়তে আসা ছাত্রছাত্রীদের। কীভাবে সুচারু পদ্ধতিতে জাতির ভিত্তিতে আলাদা করে রাখা হয় তাঁদের, নেমে আসে। শাস্তির খাঁড়া, ক্রমাগত তৈরি করা হয় বিচ্ছিন্নতা, ক্রমশই আরও প্রান্তে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা চলে প্রাতিষ্ঠানিকভাবেই।
২০০৭ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত সুখদেও থারোট কমিটি রিপোর্টে দেখা যায়, ভারতের অন্যতম অগ্রণী শিক্ষাক্ষেত্র অল ইন্ডিয়া ইনস্টিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্স (এইমস)-এ দলিত ও উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরা কীভাবে ক্রমাগত উচ্চবর্ণের শিক্ষকদের বিদ্বেষের মুখে পড়েন। এই বিদ্বেষের প্রভাব পড়ে ক্লাসের শিক্ষণে, প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় ও পরীক্ষার নম্বরে। হস্টেলে ঘেটো বানিয়ে থাকতে বাধ্য হন এই দলিত ও উপজাতি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীরা। তাঁদের ঠেলে দেওয়া হয় সেই সব হস্টেলে যেখানে শুধুমাত্র নিম্নবর্ণের ছাত্রছাত্রীদের বাস। কখনও তা হয় কর্তৃপক্ষের আদেশে, আবার কখনও উচ্চবর্ণের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা দিনের পর দিন অত্যাচারিত হয়ে তাঁরা সেখানে চলে যেতে বাধ্য হন। ব্যক্তিগত পরিসরে অন্তরঙ্গতার অভাব ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতা নিয়ে বার বার অভিযোগ জানিয়েছেন নিম্নবর্ণের ছাত্রছাত্রীরা। হস্টেলের খাবার ও রান্নাতেও আধিপত্য চলে উচ্চবর্ণের, সেই খাবারগুলোই সেখানে রান্না হয় যা উচ্চবর্ণের খাদ্য। আমাদের আরও মনে রাখা দরকার, আমাদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে রেগিং চলে তা শুধুমাত্র নতুন পড়তে আসা ছাত্রছাত্রীদের হেনস্থার একটি উপায়ই নয়, এই রেগিংয়ের মধ্যে দিয়েই চিহ্নিত করে নেওয়া হয় সেই সব ছাত্রছাত্রীদের যারা সমাজের প্রান্তিক অবস্থান থেকে পড়তে এসেছেন, দাগিয়ে দেওয়া হয় নিম্নবর্ণের ও নিম্নবর্গের ছাত্রছাত্রীদের।
২০০৭ সালে সুখদেও থোরাট রিপোর্ট প্রকাশের পর থেকে গত ১২ বছরে, দেশের অগ্রণী শিক্ষাক্ষেত্রগুলিতে আত্মহত্যা করেছেন মোট ২৩ জন দলিত ছাত্রছাত্রী। আধুনিক এই শিক্ষাক্ষেত্রগুলিতে দলিত ছাত্রছাত্রীদের এই অভিজ্ঞতার কারণ হিসাবে অনেকেই সংরক্ষণ পদ্ধতিকে দায়ী করে থাকেন। একথা ঠিক যে সংরক্ষণের ফলে আজ শিক্ষাক্ষেত্রগুলিতে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের মধ্যে তুলনামূলকভাবে বেশি সংখ্যক দলিত ও বহুজন ছাত্রছাত্রীকে দেখতে পাওয়া যায়, তবে উচ্চবর্ণরা আসলে ভয় পাচ্ছেন দলিত-বহুজন ছাত্রছাত্রীদের রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে সংগঠিত হওয়াকে। দলিত ও বহুজন ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের অধিকার বুঝে নিতে সংহত হচ্ছেন। আর তাতেই শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর উচ্চবর্ণদের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রশ্নের মুখে দাঁড়াচ্ছে। ঐতিহাসিক কাল জুড়ে পেয়ে আসা এই একচ্ছত্র অধিকার হারানোর ভয় হিংস্র হয়ে উঠছে তাঁদের প্রতিক্রিয়া। হিন্দুত্বকরণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ক্যাম্পাস গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে লাগাতার সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছেন তাঁরা। আন্দোলন গড়ে তুলেছেন ধর্মীয় ও আঞ্চলিক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নেমে আসা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দলিত খাদ্য রাজনীতিকে প্রতিষ্ঠা করতে বিফ ফেস্টিভ্যালের আয়োজন করে রেডিক্যাল বামপন্থী ও আম্বেদকারাইট অ্যাসোসিয়েশনের ছাত্রছাত্রীরা। এই অপরাধে পুলিসি হেনস্থার মুখে পড়তে হয় তাঁদের। এই ধরনের সংগঠনগুলোর উপর নেমে আসে রাষ্ট্রীয় খাঁড়া। তা আম্বেদকর স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনই হোক, বা দিল্লির দলিত আদিবাসী বহুজন মাইনরিটি স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন অথবা দেশের বিভিন্ন আইআইটিগুলোতে গড়ে ওঠা আম্বেদকর ফুলে স্টাডি সার্কেল। ছাত্র রাজনীতিকে চরমপন্থী করে তোলা, দেশদ্রোহিতা, প্রতিষ্ঠানবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ তুলে তাঁদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা চালায় রাষ্ট্র।
২০১৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ মার্চ, দেশের শীর্ষ আদালত একটি গাইডলাইন প্রকাশ করে। তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি (নিপীড়ন বিরোধী) আইনের আওতায় সরকারি কর্মচারি বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে ‘বিধিবহির্ভূতভাবে ও অবিলম্বে গ্রেফতারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এই নির্দেশনামা। ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ফ্যাসিস্ট মতাদর্শকে প্রশ্নের মুখে ফেলতে পারে এমন সবকিছুকেই বাতিল করে দিতে উদ্যত আজকের ভারত রাষ্ট্র। ইউজিসি ও মানবসম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক সহ রাষ্ট্রের প্রতিটি হাতিয়ারকে আজ তাঁরা এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহার করছে। একই উদ্দেশ্যে, নতুন ও পুরোনো দুই ক্ষেত্রেই ‘অপ্রয়োনীয়’ পিএইচডি গবেষণার বিষয়কে খতিয়ে দেখার নিদান দিতে চলেছে। রাষ্ট্র।
প্রান্তিক মানুষদের জন্য সাম্য ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তৈরি সাংবিধানিক অধিকারগুলোকে খর্ব করে, আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে দ্রুতই ব্রাহ্মণ্যবাদী এক পরিসরের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে রাষ্ট্র। ঐতিহাসিককাল ধরে শিক্ষা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ওপর উচ্চবর্ণের একচ্ছত্র শক্তি প্রতিষ্ঠার যে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রীতি চলে আসছে তারই পরিণতি আমরা দেখতে পাই পায়েল তদভি (২০১৯), রোহিত ভেমুলা (২০১৬), বালমুকুন্দ ভারতী (২০১০), এম ভেঙ্কটেশ (২০১৩), সেন্থিল কুমার (২০০৮), রেজানি এস আনন্দদের (২০০৪) মৃত্যুতে। পায়েল তদভীর মৃত্যু তাই কোনো একক ব্যক্তির সিদ্ধান্ত নয়। এটি একটি প্রাতিষ্ঠানিক হত্যা। এই মৃত্যুর কারণ, হিন্দু সমাজ জীবনে গভীরভাবে গেঁথে থাকা বর্ণবৈষম্যমূলক মানসিকতা ও জাতিবিদ্বেষ। এই হেমা আহুজা, ভক্তি মেহর ও অঙ্কিতা খাণ্ডেলওয়াল আসলে মূলধারার হিন্দু নারীবাদের প্রতিনিধি, নিম্নবর্ণের পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেই প্রতিষ্ঠিত হয় যে নারীবাদ। স্মৃতি ইরানি, কঙ্গনা রানাউত, প্রজ্ঞা ঠাকুরের গৈরিকি নারীবাদ, যা ধর্মের নামে হত্যা করে, দমন চালায় প্রান্তিকের উপর, আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে সেই নারীবাদের বিরুদ্ধে। (সূত্র : বাস্তার সলিডারিটি নেটওয়ার্ক)
ভারতে প্রতি ১৫ মিনিটে দলিত নাগরিকের উপরে একটি অপরাধ সংঘটিত হয়, প্রতিদিন ৬ জন দলিত নারী ধর্ষিত হয় এবং প্রতি বছর বস্তিতে বসবাসকারী ৫৬,০০০ শিশু অপুষ্টির দরুন মারা যায়। করোনার অতিমারির মধ্যেও উত্তরপ্রদেশের হাথরাসে ধর্ষণ, হত্যা ও মাঝরাতে দলিত ধর্ষিতার শবদেহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। উত্তরপ্রদেশ ও নৈনিতালের উচ্চবর্ণের করোনা রোগীরা আইসোলেশন কেন্দ্রে দলিত রাঁধুনির রান্না খেতে অস্বীকার করে। লকডাউনের জন্য চেন্নাই থেকে গ্রামে ফিরে এম সুধাকর তাঁর ছয় মাসের বিবাহিত স্ত্রীর সঙ্গে দেখা স্ত্রীর বাবা তাঁকে খুন করে। কারণ এম সুধাকর ছিলেন দলিত এবং তাঁর স্ত্রী ছিলেন উচ্চবর্ণের মেয়ে। ২০২০ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে ৬ তারিখে ১৭ বছরের দলিত তরুণ বিকাশ কুমার জাটভকে কেবল উত্তরপ্রদেশের আমবোহাতে মন্দিরে ঢোকার অপরাধে ৪ জন যুবক গুলি করে হত্যা করে। ২০২০ খ্রিস্টাব্দে মধ্যপ্রদেশে উঁচু জাতের জন্য রাখা খাবার স্পর্শ করার অভিযোগে বছর পঁচিশের যুবক দেবরাজ অনুরাগীকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। পুলিশ জানায় হত্যাকারী দুই যুবকের নাম যথাক্রমে সন্তোষ পাল ও ভুরা সোনি। ২০২১ খ্রিস্টাব্দে দিল্লিতে ধর্ষণ করে খুন করা হল একটি ৯ বছরের কিশোরীকে। কিশোরীর বাড়ির পাশেই শ্মশান। সেখানে কুলার থেকে ঠান্ডা জল আনতে গিয়েছিল ৯ বছরের দলিত কিশোরী। শ্মশানেই তাঁকে ধর্ষণ ও হত্যা করে কয়েকজন দুষ্কৃতি। তারপর তড়িঘড়ি পরিবারের বিনা অনুমতিতে মৃত কিশোরীকে চিতায় তুলে দেয়। পুলিশ পুরোহিত সহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে।
ভারতীয় সংবিধানে জাতিভেদ কেন্দ্রিক অস্পৃশ্যতাকে নিষিদ্ধ করেছে, বলা হয়েছে— “Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden….. ‘untouchability’ shall be an offence punishable in accordance with law”. (The Constitution of India, Part III, Fundamental Rights) এই সংবিধান মোতাবেক ভারতের সমস্ত অঞ্চলের পুণ্যতীর্থ, দেবমন্দির, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকল জাতের মানুষের কাছে সমানভাবে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। অস্পৃশ্য ও দলিত শ্রেণির মানুষ ভারতের বিভিন্ন পুণ্যতীর্থে, দেবমন্দিরে প্রবেশ করতে পারবে, শহর-নগরের পুষ্করিণী বা কূপের জল পান করতে পারবে, উচ্চবর্ণ মানুষের সঙ্গে একই বিদ্যালয়ে পাশাপাশি বসে শিক্ষালাভ করতে পারবে, একই কর্মক্ষেত্রে মিলিত ভাবে কাজ করতে পারবে, একই ভোজনালয়ে পাশাপাশি বসে পানাহার করতে পারবে। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে ভারত সরকার নিম্নবর্গের মানুষদের উচ্চবর্গে উন্নীত করার জন্য বিভিন্ন প্রকার উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা করেছে। দলিত ও তফসিলিদের (Schedule Caste) জন্য শিক্ষা ও জীবিকার ক্ষেত্রে সংরক্ষণ ব্যবস্থার প্রচলন করে তাঁদের শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি ঘটানোর প্রয়াসও রয়েছে।
কতটা বদলেছে সমাজ? কতটা বদলেছি আমরা? সময়ের সংকটে কয়েকজন যুক্তিমনষ্ক মানুষদের কিছুটা বদলালেও এখনও দলিত শ্রেণির মানুষেরা তিমিরেই পড়ে আছে। এখনও জাতির ক্ষেত্রে স্বজাতি বিবাহ শাস্ত্রসম্মত, উঁচু জাতির সঙ্গে নীচু জাতির বিবাহ গ্রহণ হয় না। আজও ব্রাহ্মণ-পুত্রসন্তান যদি কোনো শূদ্র-কন্যার বিবাহ হয় তাহলে তাঁকে শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে জাতিচ্যুত না-হলেও পরিবারচ্যুত হতে হয়। খবরের কাগজে ‘পাত্রপাত্রী চাই’ বিজ্ঞাপনে লক্ষ করুন কেমন জাতবিচারের ধূম! চূড়ান্ত বজ্জাতি। এ বজ্জাতি কি অসংবিধানিক নয়? অবশ্যই এ বজ্জাতি কি অশাস্ত্রীয় নয়? অবশ্যই। কী বলছে শাস্ত্র? একবার ফিরে দেখা যাক –“অথ ব্রাহ্মণস্য বর্ণানুক্রমেণ চতস্রো ভাৰ্য্যা ভবন্তি।১। তিস্রঃ ক্ষত্রিয়স্য।২। দ্বে বৈশ্যস্য।৩। এক শূদ্রস্য।৪।— অর্থাৎ ব্রাহ্মণ স্বর্ণ ব্যতীত অন্য তিন বর্ণের কন্যাকে বিয়ে করতে পারবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্যা ও শূদ্রাদের বিয়ে করতে পারবে; বৈশ্যেরও শূদ্রা বিবাহে কোনো আপত্তি নেই, শুধুমাত্র শূদ্ররাই শূদ্রা ভিন্ন অন্য কারোকেও বিয়ে করতে পারবে না। তার মানে উচ্চবর্ণের বিয়েতে কোনো বাছবিচার নেই, তাঁদের বিয়ে সকল বর্ণের সঙ্গে হতে পারে। তাহলে পাত্রপাত্রী চাই বিজ্ঞাপনের এত জাতপাতের বিচার কেন আজও জারি আছে। এটা কি হিন্দুদের শাস্ত্রের অবমাননা নয়? অপরদিকে শূদ্রের পাত্ররা শূদ্র ব্যতীত অন্য কোনো উচ্চবর্ণের পাত্রীকে বিয়ে করতে পারবে না। কারণ বিবাহ সূত্রে সেইসব উচ্চবর্ণের পাত্রীরা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হবে। এ ব্যবস্থা আজও মেনে চলা হয় আমাদের সমাজে। সে কারণে নিম্নবর্ণ উচ্চবর্ণে উন্নীত হতে না পরলেও সমান হতে পারল না। মনু বলেছেন– যে স্বপত্নী শূদ্রাতে ব্রাহ্মণ ঔরসে জাতা কন্যা যদি অন্য ব্রাহ্মণ বিবাহ করে এবং তার কন্যাকে যদি অপর ব্রাহ্মণ বিবাহ করে এবং এমনভাবে ব্রাহ্মণ সংসর্গ যদি ধারাবাহিক সাতপুরুষ পর্যন্ত হয়, তবে ওই বর্ণ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয় এবং এমনভাবে যেমন শূদ্র ব্রাহ্মণ হয়, তেমনই ব্রাহ্মণও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। ভুলে গেলেন ব্রাহ্মণেরা, পিছিয়ে গেলেন শূদ্রেরা। কোনো এক অনৈতিক উদ্দেশ্যে ক্রমে ক্রমে শূদ্রের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ রহিত হয়ে গেল। বললেন –“ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা ব্রাহ্মণস্য প্রকীৰ্ত্তিতাঃ।/ক্ষত্রিয়া চৈব বৈশ্যা চ ক্ষত্রিয়স্য বিধীয়তে।/বৈশ্যৈব ভাৰ্য্যা বৈশ্যস্য শূদ্রা শূদ্রস্য কীৰ্ত্তিতাঃ।” শূদ্র সমাজশরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। তাঁদের আর বর্ণান্তর প্রাপ্তির সুযোগ থাকল না।
মাঝেমাঝেই দেশনেতাদের মুখে শোনা যায়, শূদ্রদের শিক্ষার মাধ্যমে ক্রমোন্নত করাই আমাদের সমাজের লক্ষ্য। সেই আদর্শ তো ছিলই, সব ভুলে গেলেন কেন? কিরকম সেই শিক্ষা?
“ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বিশস্ত্ৰয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
শ্রুতিস্মৃতি পুরাণোক্ত ধৰ্ম্মযোগ্যাস্তুনেতরে।
শূদ্রোবর্ণশ্চতুর্থোপি বর্ণত্বাদ্ধৰ্ম্মমহতি।
বেদমন্ত্রস্বধা-স্বাহা ষষ্কারাদিভিবিনা।”
অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন জাতি দ্বিজ শব্দবাচ্য। এঁরাই শ্রুতি স্মৃতি ও পুরাণোক্ত ধর্মের অধিকারী। অন্য জাতি নয়। শূদ্রজাতি চতুর্থবর্ণ বলে ধর্মে অধিকারী, কিন্তু বেদমন্ত্র ও স্বাহা, স্বধা বষটকারাদি শব্দের উচ্চারণের অধিকারী নয়। শুধু ধর্ম বিষয়েই নয়, লৌকিক বিষয়েও শূদ্রকে কোনো উপদেশ দিতে মনু নিষেধ করেছেন এই বলে –“ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাৎ।” শাস্ত্রকারগণ খুবই ন্যায় বিচারক, ধর্মবেত্তাগণ তো সেটাই বলেন! কেমন সেই ন্যায় বিচার? চার বর্ণের একই অপরাধের শাস্তি চার প্রকারের। ব্রাহ্মণগণের সত্য দ্বারা শপথ করলেই হত, ক্ষত্রিয় অশ্ব বা আয়ুধ দ্বারা এবং বৈশ্য গো, বীজ বা কাঞ্চন দ্বারা শপথ করত, কিন্তু এত অল্পে ছাড়া যায় না। তাই শূদ্রের জন্য ফতোয়া —
“অগ্নিং বা হারয়েদেমন্দু চৈসং নিমজ্জয়েৎ।
পুত্রদারস্য বাপ্যেনং শিরাসিং স্পর্শয়েৎ পৃথক।
সমিদ্ধো ন দহত্যগ্নিরাপো নোন্মজ্জয়ন্তি চ।
ন চার্তিচ্ছতি ক্ষিপ্রং স জ্ঞেয়ঃ শপথে শুচি।”
অর্থাৎ “শূদ্রকে অগ্নিপরীক্ষা, জলপরীক্ষা কিংবা স্ত্রীপুত্রাদির মাথা স্পর্শ করে পরীক্ষা করবে। অগ্নি যাকে দগ্ধ না করে, জল যাকে না ভাসায় এবং স্ত্রীপুত্রাদির মাথা স্পর্শ করলে শীঘ্রই কোনো যন্ত্রণা ভোগ না করে –শপথ সম্বন্ধে সেই ব্যক্তিকে শুচি বলে জানবে।” শূদ্রের কী অবর্ণনীয় অবস্থা! এখন এই ব্যবস্থার প্রচলন নেই ঠিকই, একদা এহেন ব্যবস্থা প্রচলন ছিল এটা ভাবলেই তো শিউরে উঠতে নয়। মহামতি শাস্ত্রকারগণ এখানেই ক্ষান্ত হননি। নির্দয় অপরাধপ্রবণ শাস্ত্রকারগণ শূদ্রদের আগুনে পুড়িয়ে আর জলে ডুবিয়ে মেরেও। শান্তি পাননি। তাঁরা টু শব্দ করলেই শূদ্রদের হাত-পা কেটে নেওয়ার হুকুম দেওয়া হত, ব্রাহ্মণদের সঙ্গে কর্কশবাক্যে কথা বললে জিভ কেটে নেওয়ার আদেশ হত, ব্রাহ্মণকে বামনা’ ‘বিটকেল’ বলে পালালে শূদ্রকে লোহার ডাণ্ডা ছুঁড়ে মারার কথা বলা হয়েছে। শূদ্র যদি দর্পিতভাবে ব্রাক্ষণকে ধর্মোপদেশ করে, তবে রাজার উচিত কাজ সেই শূদ্রের মুখে ও কানে গরম তেল ঢেলে দেওয়া হবে, শূদ্র যে অঙ্গ ব্যবহার করে শ্রেষ্ঠ জাতি ব্রাহ্মণকে মারবে রাজা তাঁর সেই অঙ্গটাই কেটে ফেলে দেবে। শূদ্র যদি উচ্চবর্ণের সঙ্গে একাসনে বসে তবে রাজা তাঁর কটিদেশে গরম লোহার শালাকা দিয়ে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেবে, অথবা মরে না যায় এমনভাবে তাঁর পাছা দুটির মাংস কেটে দেওয়া হবে, শূদ্র যদি অহংকার করে ব্রাহ্মণের গায়ে থুতু দেয় তাহলে রাজা তাঁর ঠোঁট দুটো কেটে দেবে, ব্রাহ্মণের গায়ে প্রস্রাব করে দিলে লিঙ্গ সমূলে কেটে দেবে, ব্রাহ্মণের সামনে বাতকর্ম বা বায়ু নিঃসরণ করলে পায়ুপথ বা গুহ্যদেশ কেটে নেবে। শূদ্র যদি দ্বিজগণের ধন হরণ করে তবে প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে, শূদ্র যদি বেদ শ্রবণ করে তাহলে রাজা সিসা ঢেলে তার কান বন্ধ করে দেবে, বেদমন্ত্র উচ্চারণ করলে জিভ কেটে দেওয়া হবে। ব্রাহ্মণগণ শূদ্রদের শুধু হাতে মেরেই তুষ্ট হতে পারেননি, ভাতে মারার ব্যবস্থাও করে রেখেছেন।
“শক্তেনাপি হি শূদ্রেন ন কাৰ্য্যে ধনসঞ্চয়ঃ।
শূদ্রো হি ধনমাসাদ্য ব্রাহ্মণনেব বাধতে।”
(মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়, শ্লোক ১২৯, )
বর্ণ পিরামিডের উপরের স্তরে অবস্থানকারীরা ‘শুদ্ধ’ বলে বিবেচিত এবং তাঁদের অসংখ্য পদবি আছে। পিরামিডের নীচের অধিবাসীরা হলেন অচ্ছুৎ, তাঁদের কোনো পদবি নেই, কিন্তু অসংখ্য কর্তব্য আছে। এই শুদ্ধ এবং অচ্ছুতের বিন্যাস উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পেশা এবং বর্ণভেদভিত্তিক বিশাল ব্যবস্থার অধীনে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। এ ব্যবস্থা মানুষের উপকারী কার্যক্ষমতাকে হত্যা করে, পঙ্গু করে এবং ছিন্নভিন্ন করে দেয়। নিম্নবর্ণের মানুষদের জোর করে একঘরে করে রাখা হত। যে রাস্তা দিয়ে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা হাঁটেন সেই রাস্তা দিয়ে অস্পৃশ্যরা হাঁটতে পারতেন না। গণকুপের জল পান করতে পারতেন না, হিন্দুমন্দিরে প্রবেশ করতে পারতেন না তাঁরা, উচ্চবর্ণের স্কুলে তাদের প্রবেশাধিকার ছিল না, নিম্নবর্ণের মানুষরা ঊর্ধ্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করতে পারতেন না। আম্বেদকর যে মাহার বর্ণের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন সেটি সহ কিছু নির্দিষ্ট বর্ণের লোকেদের তাঁদের কোমরে ঝাঁটা বেঁধে রাখতে হত, যাতে হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে পায়ের ছাপ মুছে ফেলতে পারে। আর-এক নিম্নশ্রেণিকে গলায় পিকদানি ঝুলিয়ে রাখতে হত তাঁদের মুখের দুষিত লালা সংগ্রহ করার জন্য। উচ্চবর্ণের হিন্দুপুরুষের অবিসংবাদিত অধিকার ছিল অস্পৃশ্য নারীদের দেহের উপর। রামায়ণ, মহাভারত সহ প্রাচীন সাহিত্যে এরকম প্রচুর ধর্ষণের কাহিনি পাই। ভারতের অনেক অঞ্চলেই এখনও এসব ব্যবস্থা অনেকাংশে রয়ে গেছে। বর্তমান জন্মের অবাধ্যতায় শাস্তির মেয়াদ বেড়ে যাবে অর্থাৎ পরবর্তী পুনর্জন্মে আর-একবার অস্পৃশ্য অথবা একজন শূদ্র হিসাবে জন্মাতে হবে। তাই বিধিনিষেধ মানাটাই সর্বোত্তম।
শূদ্রগণ বড়োই অস্পৃশ্য। মাছ মারে বলে ধীবর ও কৈবর্তের জল অস্পৃশ্য, কিন্তু তাঁদের হাতের জলটুকু পান করলে যাঁদের জাত মারা যায়, তাঁদের কাছে পরম উপাদেয় আহার মাছ। শুড়ির হাতে মদ্য পান করলে জাত যায় না, তবে জল পান করলে জাত যায়। হাড়ি শুয়োর পালন করে বলে অস্পৃশ্য, কিন্তু হিন্দু রাজপুতেরা অনেক ক্ষেত্রেই শূয়োর ভক্ষণ করেও উচ্চশ্রেণির। নমঃশূদ্রের হাতের জল অচল, কিন্তু কারিগর কারা জেনেও বিরিয়ানি গপগপ করে খেতে কোনো প্রশ্ন ওঠে না। সোমরস পানের জন্য ব্রাহ্মণগণের তো শূদ্রই একমাত্র অবলম্বন ছিল, অবশ্য তার বিনিময়ে একটি বাছুর দেওয়া হত; সোমরস দিয়ে শূদ্র কিছুদূর যাওয়ার পর পথিমধ্যে সেই দেওয়া বাছুর কেড়ে নেওয়া হত শূদ্রের গালে চড় মেরে।
এই হল ভারতের সামাজিক ভিত। শূদ্রদের অপমানের উপর যে সভ্যতা দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে শূদ্রদের কতটা মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে পারলাম। ন্যূনতম সদিচ্ছা আছে কী? সংবিধান রচনার সময় বলা হয়েছিল আগামী ১০ বছরের মধ্যে শূদ্রের হৃত সন্মান ফিরিয়ে দিতে হবে। চাকরির ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে সংরক্ষণ দিয়ে তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতির মানুষদের সমান উচ্চতায় আনা হবে। কিস্যু হয়নি। ১৫ বছরে তো হয়ইনি, ৭৫ বছরেও হয়নি। হয়নি, কারণ সংরক্ষণের নামে ওদের নিয়ে কেবলই নোংরা রাজনীতি হয়েছে। তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতির মানুষগুলো রাজনীতির বোড়ে। এই বোড়ে চেলে উত্তরপ্রদেশের মায়াবতী যেমন মুখ্যমন্ত্রী হয়, বিহারে লালু-নিতীশরা মুখ্যমন্ত্রী হয়। তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতির মানুষদের কিছু হয় না। এই সংরক্ষণের সুবিধা প্রকৃতই যাঁদের প্রয়োজন তাঁরা অধরাই থেকে যায়, ক্রিমি লেয়ারে অবস্থিত তফসিলি জাতির মানুষ তেলে মাথায় তেল পায়। এক প্রকৃত দরিদ্র মেধাবী ছাত্রীকে নিয়ে বিডিও অফিসে গিয়েছিলাম শিডিউল কাস্ট সার্টিফিকেটের জন্য। সেখানকার অফিসার জানালেন এমন কোনো দলিল দেখাতে হবে যাতে প্রমাণ হবে যে সে ৫০ বছর আগেও শিডিউল কাস্ট ছিল।, দেখানো যায়নি। কারণ তাঁরা এতটাই গরিব ছিল যে, কোনো সম্পত্তি-সম্পদ তাঁদের ছিল না। তাই প্রমাণ করাও গেল না যে সে তফসিলি উপজাতি বাগদি সম্প্রদায়। বাগদি কি উচ্চবর্ণ! আমি নিজ দায়িত্বে তাঁকে বিনা পয়সায় উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত টিউশন দিতে পেরেছিলাম, কিন্তু সংরক্ষণের সুযোগসুবিধা নেওয়াতে পারিনি। মেধা অকালেই ঝরে গেল!
সুষ্ঠুভাবে সমাজ, সংসার মায় রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হলে কর্ম-বিভাজন অত্যন্ত আবশ্যিক, বর্ণ-বিভাজন নয়। যাকে যে কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া হবে তাঁকেই সেই কাজ করতে হবে। যে যেই কাজে দক্ষ সে সেই কাজ করবে, সেটাই স্বাভাবিক। মানবসমাজের প্রতিটি মানুষই হাতে হাত মিলিয়ে সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছেন এইভাবে। তাহলে কেন শুধু দ্বিজরাই সর্বোচ্চ সম্মান পাবে, উচ্চাসনে উপবেশনের মর্যাদা পাবে –কেন সেই মর্যাদার অংশীদার শূদ্ররাও পাবে না? কেন তাঁদের কীটাণুকীটের মতো ঘৃণা করা হবে? মানুষ কেন মানুষকে ঘৃণা করবে শুধুমাত্র ‘নিচু কাজ করার জন্য। অফিস-আদালতে বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে ‘এ গ্রুপ’ ‘বি গ্রুপ’ ‘সি গ্রুপ’ ‘ডি গ্রুপ’-এর কর্মচারীরা বিভিন্ন কাজ করেন। সন্মান ও মর্যাদাও তাই ভিন্ন ভিন্ন। এ গ্রুপ’ যেমন ব্রাহ্মণ বর্ণের মর্যাদা পায়, তেমনি শূদ্রের মর্যাদা পায় ডি গ্রুপের কর্মচারীরা। ডি গ্রুপের কাজ উপরের তিন গ্রুপের সেবা করা। এ গ্রুপের স্যারেরা নীচের দুটি গ্রুপের কর্মচারীদের কর্তৃত্ব করলেও তার সীমাবদ্ধতা আছে। ডি গ্রুপের কর্মচারীদেরকে দিয়ে সবরকম কাজ করিয়ে নিতে পারবে। জুতো পরিয়ে দেওয়া বা মুছে দেওয়া, বাজার করানো থেকে সবরকমের ফাইফরমাস করে খাঁটিয়ে নেওয়া যায়। মন চাইলে ডি গ্রুপের কর্মচারীকে কান ধরে উঠ-বোস করিয়ে দেওয়া যায়। উপরের তিন গ্রুপের বসার জন্য নির্দিষ্ট চেয়ার বরাদ্দ থাকলেও ডি গ্রুপের বসবার জন্য কোনো চেয়ার থাকে না। উপরের তিন গ্রুপের সামনে প্রায়-ক্রীতদাসের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে হয় পরবর্তী হুকুমের জন্য। ডি গ্রুপের কর্মচারীরা উপরের তিন গ্রুপের সামনের আসনে বসে পড়া বা বসে থাকা অভদ্রতা। সারা ভারতে তেমনটা না-হলেও পশ্চিমবঙ্গে সাতাত্তরে বামফ্রন্ট সরকারের শাসনকালে ডি গ্রুপের কর্মচারীদের ‘শূদ্রত্ব’ কিছুটা কাটে। বসার চেয়ার-টেবিল হয়েছে, একটা সংগঠন হয়েছে অভাব-অভিযোগ জানানোর জন্য। মর্যাদা বৃদ্ধি হয়েছে কি? না, হয়নি। আমি বেশ কয়েকটি অফিস-আদালতে গিয়ে দেখেছি উচ্চবর্ণের মানে সন্তানের বয়সি এ বি সি গ্রুপের কর্মচারীরা মা বা বাবার বয়সি ডি গ্রুপের কর্মচারীদের অবজ্ঞা-ভরা ‘তুমি’ সম্বোধন করে কথা বলেন, দুর্ব্যবহার করেন। এটা নিশ্চয় অসন্মানজনক। অফিস-আদালতেও ‘বর্ণবাদ’ অত্যন্ত সক্রিয়। ডি গ্রুপের কর্মচারীরা প্রতিনিয়ত পদদলিত হচ্ছে উপরের গ্রুপ কর্তৃক।
বৃহৎ শূদ্রসমাজকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁদের উপর শাসন ও শোষণের যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়েছিল, তা আজও অব্যাহত। হিন্দুসমাজের অধিকাংশ মানুষ গভীর নিষ্ঠা সহকারে পালন করে স্বেচ্ছায় ব্রাহ্মণশ্রেণির খবরদারি ও শোষণের বলি হয়ে চলেছে। হিন্দুসমাজে বিভেদমূলক জাতিভেদ প্রথা ও পুজো-পার্বণের মধ্য দিয়ে চিরস্থায়ী অর্থনৈতিক শোষণের ব্যবস্থা কর্তৃক সৃষ্ট হয়েছে। ভারতের মোট জনসংখ্যার ৩.৫ ব্রাহ্মণগণ এখনও রীতিমতোভাবে শূদ্রদের ভীরুতার সুযোগ নিয়ে শাসন ও শোষণ করে চলেছে। তাই শূদ্রদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকলেও তাঁরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই আছে। কারণ কাদা দিয়ে যেমন কাদা পরিষ্কার করা যায় না, তেমনি বুদ্ধিজীবী শোষকশ্রেণির নেতৃত্বে কখনও শোষণের অবসান ঘটানো গেল না। শোষণকে উচ্ছেদ করতে হলে প্রয়োজন শোষিত উৎপাদক শ্রেণির নেতৃত্ব। ডঃ আম্বেদকরের মতে, ‘জাতব্যবস্থার বিলুপ্তি’ ঘটাতে পারলেই আসবে শ্রেণি-সংগ্রাম। যাঁরা জাতকে বহাল রেখে শ্রেণি সংগ্রামের কথা বলছেন তাঁরা শ্রমজীবী মানুষদের ধোঁকা দিচ্ছে। জগজীবন রাম 761690– “Any movement for social equality must be anti Brahmin in character.” অর্থাৎ সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য যদি কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে হয় তবে তা হতে হবে ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী। ডঃ আম্বেদকরের ভাষায় –“The Brahmin is always opposed to change. For, to him change means loss of power and loss of pelf.” অর্থাৎ ব্রাহ্মণজাতি সর্বদা পরিবর্তনের বিরোধী। কারণ তাঁদের কাছে পরিবর্তনের অর্থ হল প্রভাব ও সম্পদলাভের সমূহ ক্ষতি।
ভারতে ব্রিটিশ মুক্তির পর বাবা সাহেবের তত্ত্বাবধানে তফসিলিদের জন্য যে সংরক্ষণ চালু হল, সেটার যথাযথ প্রয়োগ হল কি? না, প্রয়োগ হয়নি। চাকুরিতে কোটা হয়েছে, শিক্ষা ইত্যাদিতেও কোটা হয়েছে। কারা পাচ্ছেন এইসব সুবিধা? যাঁদের দারিদ্রতা থেকে মুক্তি হয়নি তাঁরা পেল কি? আলোকিত মানুষরা আরও বেশি করে আলোকিত হল বটে, যে বৃহৎ অংশ আঁধারে ছিল, তাঁরা আঁধারেই আছে। উল্টে সংরক্ষণ ভোগীরা সমাজে বিদ্রুপের পাত্র হয়ে গেলেন। সংরক্ষণ কোটায় চাকরি বা শিক্ষায় যাঁরা প্রবেশাধিকার পায়, তাঁদেরকে অন্যরা করুণার চোখে দেখে, তিরস্কৃত হয়। এই সংরক্ষণ আসলে সমাজকে বিভাজিত করে রাখল, একত্রিত করতে পারেনি। ব্রাহ্মণ্যবাদের এই সুচতুর কৌশলে ১০০ ভাগ ব্যর্থ হয়ে গেল বাবা সাহেবের স্বপ্ন। আজও, এখনও উচ্চবর্ণেরা মায় নিম্নবর্ণ পর্যন্ত কোনো চিকিৎসকের নামের পিছনে দাস-মণ্ডল বিশ্বাস পদবি থাকলে তাঁর কাছে চিকিৎসা করাতে দ্বিধা বা কুণ্ঠাবোধ করে। কম নম্বর পেয়েও বিশেষ কোটায় প্রাপ্ত চাকরি বা পেশায় যুক্ত ব্যক্তিকে অযোগ্য কম শিক্ষিত ভাববে এটা আর নতুন কী! তাঁর জ্ঞান তাঁর দক্ষতা নিয়ে তো প্রশ্ন ওঠবেই। ভাবতে অবাক লাগে দাস-মণ্ডল-বিশ্বাস পদবিধারী চিকিৎসকদের তথাকথিত নিম্নবর্গের রোগীরাও সহসা চিকিৎসা করাতে চান না। তাঁদের মোহ আজও ব্যানার্জি-চ্যাটার্জি-মুখার্জি পদবিধারী চিকিৎসকদের প্রতি ধাবমান।
হার্দিক পটেলের মামলায় গুজরাত হাইকোর্টের বিচারপতি জে বি পর্দিওয়ালা সংরক্ষণের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছিলেন। ওই মামলায় রায় গিতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন, “দুটি জিনিস দেশকে ধ্বংস করে দিয়েছে। বা বলা ভাল, দেশকে সঠিক পথে এগোতে দেয়নি। এক, সংরক্ষণ, দুই, দুর্নীতি।” সংরক্ষণের বিরুদ্ধে ‘অসাংবিধানিক’ মন্তব্য করায় গুজরাত হাইকোর্টের এই বিচারপতিকে ‘ইমপিচ করা অর্থাৎ সরিয়ে দেওয়ার দাবি উঠেছিল সংসদে। যে ৫৮ জন সাংসদ চেয়ারম্যানকে দেওয়া পিটিশনে সই করেছেন, তাঁদের মধ্যে কংগ্রেস, সিপিএম, সিপিআই, জেডি(ইউ), বিএসপি, ডিএমকে, এনসিপি –সব দলের সদস্যই ছিল। তবে তৃণমূল কংগ্রেসের কেউ ছিল না। কংগ্রেসের তরফে আনন্দ শর্মা, অশ্বিনীকুমার, অস্কার ফার্নান্ডেজ, অম্বিকা সোনি, বি কে হরিপ্রসাদ, সিপিআইয়ের ডি রাজা, সিপিএমের কে এন বালগোপাল, জেডি(ইউ)-র শরদ যাদবরা ওই পিটিশনে সই করেছিলেন। গুজরাতের বিচারপতির বিরুদ্ধে পিটিশনে বলা হয়েছে –বিচারপতি পর্দিওয়ালা হার্দিক পটেলের মামলার রায়ে বলেন, “যখন সংবিধান তৈরি হয়েছিল, এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল যে দশ বছরের জন্য সংরক্ষণ প্রথা বজায় থাকবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হল, স্বাধীনতার ৬৫ বছর পরেও সংরক্ষণ চলছে।” সাংসদের যুক্তি, “সংবিধানে দশ বছরের রাজনৈতিক সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। সেটি সংসদ বা বিধানসভায় তফসিলি জাতি উপজাতির জন্য সংরক্ষণের বিষয়। তার সঙ্গে শিক্ষা বা চাকরিতে সংরক্ষণের সম্পর্ক নেই। একজন বিচারপতি যে তফসিলিভুক্ত মানুষের সংরক্ষণের বিষয়ে অবহিত নন, সেটা দুর্ভাগ্যজনক।”
তবে কি সংরক্ষণ শুধু রাজনৈতিক, চাকুরি আর শিক্ষায় সীমাবদ্ধ থাকবে? সমাজে সাম্যতার প্রয়োজন নেই? সমাজে সাম্যতার জন্য ভোট-রাজনীতিকরা কী কী প্রকল্প ভেবেছেন? ভাবেননি, ভাবলে আজও দলিত শ্রেণির মানুষ অপমানিত হত না, নির্যাতিত হত না, লাঞ্ছিত হত না, ধর্ষিত হত না, তদুপরি ছোটোজাতের মানুষ হয়ে জীবন ধারণ করতে হত না।
ভোট-রাজনীতি বা ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে উঠে এল কাঁসিরামের দলিত সম্প্রদায় (বহুজন সমাজ পার্টি বা বিএসপি)। খুব সহজ ছিল না সেই যাত্রাপথ। ত্রয়োদশ লোকসভা নির্বাচনে সবচেয়ে বড়ো চমক ছিল মায়াবতী এবং মুলায়ম সিং যাদব। প্রচারের আলো মুলায়মের উপর কিছুটা পড়লেও মায়াবতী অন্ধকারে। দলিত মায়াবতীকে পদে পদে হেয় এবং হাস্যাস্পদ করে বর্ণহিন্দুর সমাজ-রাজনীতি-গণমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে সার্থক করতে চাইছিল। মিডিয়ার উপেক্ষা, উপেক্ষা এবং অবশ্যই অপেক্ষা। মায়াবতীকে ধর্তব্যের মধ্যেই রাখল না কেউ। বস্তুত কারোকে হেয় করার পক্ষে উপেক্ষার চেয়ে আর কোন্ অস্ত্র সর্বাধিক ধাঁরালো হতে পারে? কিন্তু সেই অমোঘ উপেক্ষাকে অগ্রাহ্য করে মায়াবতী একাই ছুটলেন তাঁর রাজ্যের ৮৫টি লোকসভা কেন্দ্রের প্রতিটি কোনায় কোনায়। রাস্তার ধুলো উড়িয়ে তাঁর মোটরগাড়ি এক সভাস্থল থেকে অন্য সভাস্থলে ছুটে গেছে। গোরুর গাড়ি ছাড়া অন্য কোনো গাড়িতে চড়তে অভ্যস্ত দলিতরা তাঁদের নেত্রীর এই মোটরগাড়ি চড়া দেখে গর্বিত বোধ করেছে। “ভোট হামারা রাজ তুমহারা, নেহি চলেগা নেহি চলেগা”— অবশেষে ব্রাহ্মণ্যবাদ তথা শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এসে গেল দলিত শ্রেণির চোখ-ধাঁধানো সাফল্য। তিলতিল করে গড়ে তোলা নিজেদের গণভিত্তি ধরে রাখতে পেরেছিল মায়াবতীর বিএসপি। তৎসহ তাঁদের বার্তা সম্প্রসারিত করতে পেরেছিল নতুন নতুন জনগোষ্ঠীর মধ্যে। দলিত মায়াবতী অত্যন্ত নিপুণ চাতুর্যের সঙ্গে পাটিগণিতের মিশেল ঘটিয়ে ক্ষমতার অলিন্দে চলে এলেন, সদলবলে। বৰ্ণহিন্দুদের আধিপত্য খর্ব হল, দলিত শ্রেণির ক্ষমতায়ন হল।
এখন প্রশ্ন– শুধুমাত্র দলিতের ভোটেই ক্ষমতার অলিন্দে আসা সম্ভব? না, নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। যে পার্টি শুধুমাত্র দলিতদের জন্য, সেই দলকে উচ্চবর্ণের ভোটাররা ভোট দেবে কেন? দেবে, কারণ রাজ্যের জনবিন্যাসের কাঠামোয় সম্প্রদায় ও জাতের অনুপাত অনুযায়ী তিনি ৩৮ শতাংশ অনগ্রসর, ২০ শতাংশ দলিত, ১৭ শতাংশ মুসলিম এবং ১০ শতাংশ উচ্চবর্ণীয় প্রার্থীকে টিকিট দিয়েছিলেন মায়াবতী। আসন বণ্টনেই বাজিমাত করেছিলেন মায়াবতী। যুদ্ধের অর্ধেক জয় এখান থেকেই শুরু। প্রজাতন্ত্রের সমগ্র অতীত ইতিহাসে যেসব ‘ছোটোজাত’ ‘অস্পৃশ্য’রা বুথের ধারেকাছে ঘেঁষতে পারত না, সেই ছোটোজাতরাই লোকসভার আসনগুলি অলংকৃত এবং আলোকিত করে রাখলেন।
এতদসত্ত্বেও মায়াবতীর স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপে দলিতরা শেষপর্যন্ত অনাস্থা জ্ঞাপন করলেন। কারণ মায়াবতীরা সুশাসনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেননি। নন্দিত নয়, বরং নিন্দিত হলেন দেশজুড়ে। কারণ ক্ষমতার গোলকধাঁধায় মায়াবতীরাও ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিলিপি হয়ে উঠলেন। ক্রমে ক্রমে মায়াবতীও ‘দেবী’ হলেন, মানে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুকরণে ‘ঈশ্বর হয়ে গেলেন। রাজ্যের দিকে দিকে ‘দেবী’ মায়াবতীর মূর্তি হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। জাস্ট ব্রাহ্মণ্যবাদের অন্ধ অনুসরণ করলে শাসনের নতুন ধারা পাবেন কীভাবে দলিতরা? উল্টে ব্রাহ্মণ্যবাদ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে উত্তরপ্রদেশে। ভাবলে অবাক লাগে উত্তরপ্রদেশের দলিত শ্রেণি থেকে উঠে আসা ধনী মুখ্যমন্ত্রী মায়াবতী যখন দলিতদের জন্য কোনো মঙ্গলই করতে পারেন না। উল্টে তিনি তাঁর আইপিএস অফিসারকে দিয়ে নিজের জুতো পরিষ্কার করান, মাথার উপর এসি নিয়ে মিটিং মিছিল করেন ইত্যাদি। আহা, মর্যাদার কী অপচয়! অথচ কাঁসিরামের বহুজন সমাজ পার্টি এই উত্তরপ্রদেশেই যখন শাসনক্ষমতার অংশীদার হন তখন সর্বজনীন ভোটাধিকারের সুযোগ সদ্ব্যবহার করে দলিত-অনুসূচিতরাও যে ক্ষমতা দখল করতে পারে তা কাঁসিরাম হাতেকলমে প্রমাণ করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। দেশব্যাপী নিম্নবর্গীয় সমাজের গ্লানি ও হীনম্মন্যতা যেমন অনেকাংশে কেটেছে, উজ্জীবিত করেছে। দলিত শ্রেণি তো শুধুমাত্র উত্তরপ্রদেশেই নেই, ভারতের সমস্ত রাজ্যেই তাঁরা বিপুল সংখ্যায় আছেন– তা সত্ত্বেও কাঁসিরামের দল ‘বহুজন সমাজ পার্টি’ অন্য কোনো রাজ্যে বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলতে পারেননি। শূদ্র জাগরণ তো দূর-অস্ত? ভোটে রাজনীতিতে জাগরণ না-হলেও সামাজিক জাগরণে বাধা কোথায়? সামাজিক জাগরণে ব্যর্থ হল কাঁসিরামের দলিত বহুজন সমাজ পার্টি বা বিএসপি।
বাবাসাহেব আম্বেদকর থেকে জগজীবন রাম, মায়াবতী থেকে শিবু সোরেন– সকলেই হয় জাতীয় কংগ্রেস, না-হয় বিজেপির খপ্পরে গ্রাসিত হয়েছেন। ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের যিনি ঝড়-বৃষ্টি-অগ্নি, সেই দলিত শিবু সোরেন পর্যদস্ত হলেন জাতীয় রাজনীতিকদের ষড়যন্ত্রে। কেন্দ্রের ইউপিএ জোট সরকারের তিন শরিক দল– জেএমএম, কংগ্রেস ও আরজেডির কোয়ালিশন সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শিবু সোরেন। শিবু সোরেন আগে ছিলেন কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রী। অবশেষে শিবু সোরেনও বর্ণহিন্দুদের ফাঁদে শরীর ডোবালেন। দুর্নীতি ও খুনের মামলায় তাঁকে পদত্যাগ করতে হল। বিচারে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার পর তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হন। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার জোট সরকারে ক্রিমিনাল রেকর্ড আছে এমন বিধায়কের সংখ্যা ৩১। এদের নিয়েই নতুন ঝাড়খণ্ড সরকার গড়বেন দলিত শিবু সোরেন। সে কথা ঘোষণা করতে এসে বড়ো মুখে বললেন। দুর্নীতিমুক্ত সরকার জনসাধারণকে উপহার দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য। ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নিজেরই ১৮ জন বিধায়কের মধ্যে ১৭ জনের নাম দাগি আসামি হিসাবে পুলিশের খাতায় জ্বলজ্বল করছে। একমাত্র ক্রিমিনাল রেকর্ডহীন বিধায়ক শিবু সোরেনের পুত্রবধূ প্রয়াত দুর্গা সোরেনের স্ত্রী সিতা সোরেন। শিবুর বিধায়কদের মধ্যে সর্বোচ্চ অপরাধের অভিযোগটি আছে জগন্নাথ মাহাতোর নামে। তাঁর নামে দায়ের করা আছে ১৪টি অপরাধ। শিবুর ছেলে হেমন্ত সোরেনের নামে আছে ৬টি অপরাধের অভিযোগ। জেএমএম ছাড়াও জোট সঙ্গীদের মধ্যে আছেন বাকি ১৪ জন বিধায়ক, যাঁরা নরহত্যা সহ বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত।
শিবু সোরেনও দলিতদের নিয়ে ঝাড়খণ্ড বানালেন, মুখ্যমন্ত্রী হলেন। ব্রাহ্মণ্যবাদের অন্ধ অনুসরণ করলেন এবং পুনরায় পতিত হলেন। ঝাড়খণ্ড এবং শিবু সোরেন আদিবাসী চেতনায় একটি সমার্থক শব্দ হওয়া সত্ত্বে পতন হল। বর্ণবাদের বিষ বড়োই ভয়ানক। শিবু সোরেনরা কখনোই অরণ্যের অধিকার, মাটির অধিকার, জলের অধিকার, আকাশের অধিকার, বাতাসের অধিকার অর্জন করতে পাবে না? ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের মসৃণ অগ্রগতির পথ থেকে অস্পৃশ্যদের সরে যেতেই হবে! ষড়যন্ত্র আর প্রতারণার শিকার হবে! শম্বুক, একলব্যরা চিরকাল হননযোগ্য হয়েই থাকবে?
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থ ‘জাতের বিড়ম্বনা’য় বলছেন –“স্মৃতিশাস্ত্রকে এখন রান্নাঘরের হাঁড়িকুঁড়ির শাস্ত্র বলিলেই চলে। রন্ধনটা যে ব্রাহ্মণের একটা বিশেষ কাৰ্য্য একথা সেকালের ধৰ্ম্মশাস্ত্রকারেরা লিখিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের একালের পণ্ডিত মহাশয়েরা সে ভুলটা সংশোধন করিয়া লইয়াছেন। এখন বামুন ঠাকুর, অর্থে রাঁধুনি। আজকাল ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতের ভাত খাইলে আমাদের ঠাকুর মহাশয়দের এক তাল গোবর খাইয়া সে ভাত হজম করিতে হয়। কিন্তু সেকালে ব্রাহ্মণদের এতটা অজীর্ণ হয় নাই। ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের অন্নের ত কথাই নাই; অনেক শূদ্রের হাতের ভাতও তাঁহারা নির্বিবাদে হজম করিতেন। তাঁহাদের জাতটি যে তাহাতে মারা যাইত, এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। আজকাল আহার বিষয়ে যিনি যত বড়ো ‘ছুৎমার্গী’, তিনি তত বড়ো পণ্ডিত।”
কিন্তু কী আশ্চর্য! অস্পৃশ্যের অজুহাতে যে ঘৃণা যে প্রকার উচ্চবর্ণেরা করে থাকে তা মূল শাস্ত্রীয় বিধিতে পাওয়া যায় না। লৌকিক যুক্তিও নেই। যা আজকাল চল আছে তা হল অহংকারপ্রসূত দেশাচারমাত্র। শাস্ত্রে যা নির্দেশ আছে তা নিশ্চয় কার্যকর হয় না। মুচি বা ঢুলি বা চর্মশিল্পী গোরু-ছাগলের ছাল ছাড়ায় বলে তাঁরা খুবই ঘৃণ্য, কিন্তু তাঁদের তৈরি তবলা-ঢোলক ব্যবহার করলে ঘৃণ্য হই না, টিউবওয়েলে গোরুর চামড়ার ওয়াশার ধোয়া জল খেলে জাত যায় না। নমঃশূদ্রের জল অচল— মুসলমানের বরফ, ডাবের জল, খাসির মাংস, বিরিয়ানি খেলে জাত যায় না। যদিও একটা পর্যায়ে মুসলমানরাও ভয়ানক অচ্ছুৎ ছিল। আজও নেই সে কথা বলা যায়ে না। আসলে হিন্দুসমাজের চোখে মুসলমানেরাও তো দলিত শ্রেণিই। দলিত খ্রিস্টান কিংবা দলিত মুসলিমদের ধারণাটি আপাতদৃষ্টিতে স্ববিরোধী বলে মনে হতে পারে। ভারতে মতো দেশে দলিতরাই প্রধানত খ্রিস্টান বা ইসলাম ধর্মে অন্তরিত হয়েছেন। অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদপীড়িত হিন্দুসমাজের নিম্নবর্গীয় জনসমাজই সাম্য ও সৌভ্রাত্রের আকর্ষণে একদিন হিন্দুধর্ম ছেড়ে ইসলামকে বরণ করেছিলেন। বরং বলা ভালো– হিন্দুধর্মে তাঁরা কখনোই সেভাবে আঁকড়ে ধরার সুযোগই পাননি, ধর্মধ্বজাধারীরা ও সমাজপতিরা কাঁটাতারের ওপারেই রেখে দিয়েছিলেন। দলিত হিন্দুরাই যে ধর্মান্তরিত হয়ে ভারতীয় মুসলমান কিংবা খ্রিস্টান হয়েছেন, এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য। যেহেতু সেই দলিতই আজকের মুসলিম, তাই মুসলমানও অস্পৃশ্য। কিন্তু দলিত হয়েও ভারতীয় খ্রিস্টানরা কী আদরনীয়? ২৫ ডিসেম্বর বড়োদিন এবং ফার্স্ট জানুয়ারি হিন্দুদের উল্লাসে কোনো খামতি দেখি না। ঘরে ঘরে সান্তাক্লজ এসে মোজায় উপহার দিয়ে যাওয়ার নিয়ম পালন করে, কেক খান। কিন্তু ইদের দিনে কোনো হিন্দুকে দেখিনি বিরিয়ানি-ফিরনি খেতে। ডাবল স্টান্ডার্ড মানসিকতা কেন? মর্মান্তিক হলেও সত্য, ইসলাম বা খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেও ভারতীয় দলিত ও জনজাতীয়রা আগের মতো প্রান্তিক হয়ে থেকে গেছেন। নতুন সম্প্রদায় হয়েও জাতে উঠতে পারল না ভারতীয় সমাজে।
জাতপাত ব্যবস্থা বর্ণগত মই বাহিত হয়ে নিচে নেমে যায় এবং কখনোই পুরোপুরি অদৃশ্য না-হওয়ায় আম্বেদকরের বর্ণিত ‘অনুকরণের সংক্রমণ’ প্রতিটি বর্ণেরই ক্রমপরম্পরায় নিম্নতর বর্ণের উপর আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা হয়। তেজস্ক্রিয় অণুর অর্ধেক জীবনের মতো ‘অনুকরণের সংক্রমণ’ গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করার সুযোগ নষ্ট করে দেয়। এর ফলে এমন এক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটেছে যেটাকে আম্বেদকর বলেছেন ‘ক্রমবিন্যস্থ বৈষম্য’। এতে আরও নিচুর তুলনায় নিচু বর্ণও বিশেষ অধিকার ভোগের অবস্থানে থাকে। প্রতিটি বর্ণই বিশেষ অধিকার ভোগ করে, প্রতিটি শ্রেণিই ব্যবস্থাটি বজায় রাখার ব্যাপারে আগ্রহী। আমাদের সমাজে পচনের মূলেই আছে এই জাতপাত প্রথা। অধস্তন জাতের প্রতি যা কিছু করা হয়েছে, তা তো আছেই, সেইসঙ্গে এটা বিশেষ অধিকারভোগকারী বর্ণের নৈতিকতার মূলে পচন ধরিয়েছে।
ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর মতে, প্রতি ১৬ মিনিটে একজন দলিতের সঙ্গে আর-একজন অদলিত অপরাধ করে, প্রতিদিন ৪ জনেরও বেশি অস্পৃশ্য নারী স্পৃশ্যদের দ্বারা ধর্ষিত হয়। প্রতি সপ্তাহে ১১ জন দলিত খুন হয় এবং ৬ জন দলিত অপহৃত হয়। শুধুমাত্র ২০১২ খ্রিস্টাব্দেই ২৩ বছর বয়েসের ১ জন নারী দিল্লিতে গণধর্ষণের শিকার হয়, ১৫৭৪ জন দলিত নারী ধর্ষিত হয় (বৃদ্ধাঙ্গুলির শাসানির জোরে দলিতদের সঙ্গে ঘটা ধর্ষণ বা অন্যান্য অপরাধের মাত্র ১০ ভাগ প্রকাশিত হয়) এবং ৬৫১ জন দলিতকে হত্যা করা হয়। এগুলি ছিল ধর্ষণ ও বর্বরতা, যা লুণ্ঠন আর নগ্ন হতে বাধ্য করাই নয়, জোরপূর্বক মানুষের মল খাওয়ানো, জমি দখল, সমাজচ্যুত করা, খাওয়ার জল আনতে বাঁধা দেওয়া। এ পরিসংখ্যানে পাঞ্জাবের বান্ত সিংয়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি, যিনি ছিলেন একজন মাজহাবি দলিত শিখ। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দে যার দুই হাত এবং একটি পা কেটে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে দেওয়া হয়। কারণ সে তাঁর মেয়েকে গণধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করার দুঃসাহস দেখিয়েছিল। তিনটি অঙ্গ ছেদ হওয়া ব্যক্তির জন্য আলাদা কোনো পরিসংখ্যান নেই। কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে—
ঘটনা– ১: ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর। মধ্যপ্রদেশ। তার খেতে ঢুকে ফসল খেয়ে নিচ্ছিল গরুর দল। গোরুর মালিককে এ ব্যাপারে অভিযোগ জানাতে গিয়ে চরম লাঞ্ছনার শিকার হতে হল এক দলিত নারীকে। তাঁকে নগ্ন করে মারধরের পর প্রস্রাব খেতেও বাধ্য করা হয়। ছত্তরপুর জেলায় এই নৃশংস ঘটনা ঘটেছে। এই ঘটনায় স্থানীয় থানার নিষ্ক্রিয়তার বিষয়টিও প্রকাশ্যে এসেছিল। ওই মহিলাকে নিয়ে দলিত সম্প্রদায়ের কয়েকজন জেলার সহকারী পুলিশ সুপার নিরজ পান্ডের সঙ্গে দেখা করেন। তাদের অভিযোগ, স্থানীয় নওগং থানা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না। নিগৃহীতার অভিযোগ, বিজয় যাদবের বাড়িতে গিয়ে তার খেতে গোরু ঢোকার বিষয়টি জানান। আর এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে বিজয় ও তার স্ত্রী বিমলা তাঁকে মারধর করেন। এমনকি জামাকাপড় খুলে তাকে প্রস্রাব খেতেও বাধ্য করা হয়।
ঘটনা– ২ : ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ১১ অক্টোবর। উত্তরপ্রদেশ। এক দলিত পরিবারের পুরুষ ও নারীদের প্রকাশ্যে নগ্ন করে পেটাল পুলিশ। সন্তান ও লোকজনের সামনে এই দম্পতিকে নগ্ন করার ঘটনা ঘটল। বুদ্ধনগর জেলার ধানকুড় থানায় এই ঘটনা ঘটে। স্থানটি ভারতের রাজধানী দিল্লি থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। ঘটনার দিন ধানকুড় থানায় একটি ডাকাতির মামলা করতে যান সুনীল গৌতম নামে একজন দলিত পুরুষ। পুলিশ ওই মামলা না-নিয়ে স্ত্রীসহ সুনীলকে বাজারে রাস্তার মধ্যে কাপড় খুলে সম্পূর্ণ নগ্ন করে দাঁড় করিয়ে রাখে। এরপর নগ্ন দম্পতিকে পেটায়। এ ঘটনার পর স্থানীয় এক সাংবাদিক পুরো ঘটনাটির একটি ভিডিও বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করেন। প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, সাধারণ পোশাক পরা এক ব্যক্তি রাস্তায় দাঁড় করিয়ে ওই দম্পতির কাপড় টেনে ছিঁড়ে ফেলছে। আর পাশেই দাঁড়িয়ে ঘটনাটি দেখছে পুলিশের পোশাক পরা এক ব্যক্তি। কিছুক্ষণ পর সেই পুলিশও মারধরে অংশ নেয়। ঘটনা প্রকাশ পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত দুজনকে পুলিশ বলে চিহ্নিত করেছেন ওই দলিত দম্পতি।
ঘটনা– ৩ : ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মে। উত্তরপ্রদেশ। শাহজানপুর জেলার জালালাবাদের কাছে একটি গ্রামের অন্তত পাঁচজন দলিত মহিলা অভিযোগ করেছেন, তাঁদের চেয়ে তুলনায় উঁচু জাতের কাশ্যপ সমাজের অন্তত পনেরো জন নারীপুরুষ সেদিন সকালে তাঁদের উপর চড়াও হয়। তারপর তাঁদের কাপড়চোপড় খুলে নিয়ে রাস্তা দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হয়। এসময় তাঁদের বেত দিয়ে পিটনো হয়। বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে চলে এই নির্যাতন। দলিত সমাজের একটি ছেলে কাশ্যপদের একটি নাবালিকা মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার অভিযোগে তাঁদের উপর এই নির্যাতন চালানো হয়। ওই মেয়েটির মা এবং অন্য আত্মীয়রা এসে ছেলেটির মা-নানি-চাচিদের উপর হামলা চালান। তাঁদের মারধর করা হয়, শাড়ি ও কাপড়চোপড় খুলে নেওয়া হয়। এসময় হামলাকারীরা বলতে থাকেন- “আমাদের সম্মান যাঁরা নষ্ট করেছে তাঁদের আবার ঘোমটা কীসের, তাঁদেরকেও আমরা ইজ্জত রাখতে দেব না।” ঘটনার তদন্তে যে প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিলেন তাঁরা এসে রিপোর্ট দিয়েছেন দলিত মহিলাদের অবশ্যই নগ্ন করে ঘোরানো হয়েছিল। এসময় প্রশাসনও প্রথমে নির্বিকার ছিল। তবে জানা গেছে দলিতদের বে-ইজ্জতি করার জন্য কাশ্যপ সমাজের মোট দশজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। এঁদের মধ্যে চারজন পুরুষ ও তিনজন মহিলাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আরও তিনজন পলাতক মহিলাকে ধরার জন্য বিশেষ দলও গঠন করা হয়েছে।
ঘটনা– ৪ : ২০১২ খ্রিস্টাব্দের ১৩ জানুয়ারি। মহারাষ্ট্র। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ চ্যবনের নিজ জেলায়ই এক মহিলাকে নগ্ন করে রাস্তায় ঘোরানো হয়েছে। এ ঘটনার আগে ৪৫ বছর বয়সি ওই নারীকে একদল মানুষ প্রহার করে। এসব ঘটনার পর তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। দলিত শ্রেণির ওই মহিলা এখন বিচার চাইছেন সবার কাছে। কিন্তু তিনি দলিত শ্রেণির বলে তাঁর অভিযোগ নিবন্ধিত করতে বিলম্ব করা হয়। অভিযোগ আছে, ওই ঘটনায় জড়িতরা মুখ্যমন্ত্রীর খুব কাছের বলে তাঁদের বিরুদ্ধে মামলা নিতে বিলম্ব করা হয়। তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপও নেওয়া হচ্ছে না। ২০১১ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ডিসেম্বর উচ্চবংশীয় এক যুবতাঁকে নিয়ে পালিয়ে যায় নির্যাতিত ওই দলিত মহিলার ছেলে। এরপর ওই যুবতীর অভিভাবকরা তাঁদের মেয়ে নিখোঁজ হয়েছে। মর্মে একটি অভিযোগ দাখিল করে। একই সঙ্গে তাঁরা ওই মহিলাকে তাঁদের মেয়ে বের করে দিতে নানাভাবে হয়রানি করতে থাকে। ওই সময় তিনি জানিয়ে দেন তাঁর ছেলে ও ওই মেয়ে পালিয়ে কোথায় গেছে তা তিনি জানেন না। নিখোঁজ যুবতীর পরিবার একটি স্থানে ডেকে নেয় দলিত শ্রেণির ওই মহিলাকে। এরপর তাঁকে প্রশ্নবাণে তাঁরা জর্জরিত করতে থাকে। এক পর্যায়ে। তাঁরা তাঁকে ধমকাতে থাকে, প্রহার করতে থাকে, এমনকি তাঁকে নগ্ন করে গ্রাম ঘুরতে বাধ্য করে। এ ঘটনায় ওই মহিলা মারাত্মক আহত হন। তাঁকে পরের দিন একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দলিত মহাসংঘ প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাচিন্দ্র সাকাতে বলেছেন, “মুখ্যমন্ত্রীর নিজের জেলায় এ ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় কর্তৃপক্ষ চোখ বন্ধ করে আছে। তাঁরা রাজনৈতিক কারণে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না।”
ঘটনা– ৫: ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের ২৩ জানুয়ারি। পশ্চিমবঙ্গ। কুড়ি বছরের এক আদিবাসী তরুণীকে ১২ জন ব্যক্তি গণধর্ষণ করেছে বীরভূম জেলায়। গ্রামে সালিশী সভায় ওই তরুণীকে ‘অপরাধী’ বলে চিহ্নিত করে গণধর্ষণের শাস্তি দেওয়া হয়। ওই মেয়েটির ‘অপরাধ’ অনাদিবাসী একটি ছেলের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্ক ছিল গত পাঁচ বছর ধরে। গ্রামের মোড়ল ও ধর্ষণকারী সহ মোট ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বীরভূমের পুলিশ প্রধান সি সুধাকর জানিয়েছেন, “সোমবার রাতে রাজারামপুর গ্রামে সালিশী সভায় ওই গণধর্ষণের নির্দেশ দেন গ্রামের মোড়ল বলাই মান্ডি। অভিযোগে বলা হয়েছে, চৌহাট্টা গ্রামের এক অনাদিবাসী ছেলের সঙ্গে অত্যাচারিতা ওই মেয়েটির প্রেমের সম্পর্ক জানাজানি হয়। সেদিনই সালিশী সভায় দুজনকে অপরাধী বলে চিহ্নিত করা হয় আর ২৫০০০ টাকা করে জরিমানা ধার্য করা হয়। যুবকের পরিবার টাকা। মিটিয়ে দিতে পারলেও ওই তরুণীর পরিবার তাঁদের আর্থিক অবস্থার কথা জানিয়ে টাকা দিতে পারবে না বলে জানায় গ্রামের প্রধানদের। তখনই মোড়ল বলাই মান্ডি বলে “যাও, ওকে নিয়ে মজা করো”। পরপর ১২ জন ধর্ষণ করে তরুণীটিকে, যাঁদের মধ্যে মেয়েটির বাবার বয়সি লোকও ছিল, আবার তাঁর ভাইয়ের বয়সি ছেলেও ছিল। প্রধান বলাই মান্ডি আবার ওই তরুণীর গ্রাম সম্পর্কে কাকা। ২০১০ খ্রিস্টাব্দে এক তরুণীকে নগ্ন করে গ্রামে ঘোরানো হয় এক যুবকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কের কারণে। আদিবাসী সমাজে অনাদিবাসী। কাউকে বিয়ে করলে সমাজচ্যুত করার চল রয়েছে। এ হল দলিত কর্তৃক দলিতের লাঞ্ছনা।
ঘটনা– ৬ : ২০১৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুলাই। আসাম। ডাইনি সন্দেহে এক বৃদ্ধাকে নগ্ন করে শিরোচ্ছেদ করা হয়েছে। আসামের সোনিতপুর জেলায় আদিবাসীদের একটি গ্রামের এ ঘটনায় পুলিশ দুজন মহিলা সহ সাতজনকে আটক করেছে। পুলিশের স্থানীয় এক কর্মকর্তা সামাদ হুসেন বলেন, ওই গ্রামে গত কিছুদিন ধরে অসুখ-বিসুখ ছড়িয়ে পড়ছিল। এর জের ধরে গ্রামবাসীরা ৬৩ বছর বয়সি পুরনি ওরাংকে দায়ী করা শুরু করে। এক পর্যায়ে তাঁরা ওই বৃদ্ধাকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে শিরোচ্ছেদ করে। প্রসঙ্গত, আসামে অনেক আদিবাসী সমাজে এবং চা শ্রমিকদের মধ্যে মহিলাদের ডাইনি হিসাবে সন্দেহ করার চল রয়েছে। গত বছর অক্টোবর মাসে দেবযানী বোরা নামে ভারতের জাতীয় পর্যায়ের অ্যাথলেটকে ডাইনি হিসাবে অভিযুক্ত তাঁকে বেদম মারধর করা হয়। রাজ্য পুলিশের দেওয়া হিসাবে, গত ছয় বছরে ডাইনি সন্দেহে আসামে ৯০ জনকে হয় মাথা কেটে নেওয়া হয়েছে অথবা জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে।
২০০৫ খ্রিস্টাব্দে ৩১ আগস্ট হরিয়ানার গোহানায় বর্ণহিন্দুদের জনাকয়েক ক্ষমতাবান লোক দলিতদের একটি বস্তির ডজনখানেক বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে। সরকার থেকে ঘোষণা করা হল পুড়ে যাওয়া বস্তির প্রত্যেককে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। কিন্তু অন্যায় কাজটি যাঁরা করল তাঁদের কী শাস্তি হল কেউ জানে না। হরিয়ানায় যখন দলিতদের বস্তি পুড়ে ‘রাখ’, ঠিক তখনই বিহারে রণবীর সেনাদের গুলিতে ঝাঁঝরা দলিত মানুষেরা। এ-রকম না-হলেও অন্যরকম হতে বাধা কোথায় পশ্চিমবঙ্গে! তমলুক শহরের পদুমপুর গ্রামের তফসিলিভুক্ত পরিবারগুলি মন্দিরে ঢুকতে পারে না।পঞ্চায়েতের সিপিএম সদস্য প্রভাস ধাঁড়া স্বীকার করেছেন, গ্রাম কমিটির নামে মোড়লদের দাপট এখানে এতটাই বেশি যে অনেকবার বৈঠক করেও তফসিলিদের মন্দিরে ঢোকার ব্যবস্থা যায়নি। ফলে তফসিলি পরিবারগুলি পুজো দেওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত।” এ-সময়। রাজ্যের তখত-এ-তাউসে উপবিষ্ট কমঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।
বর্ণহিন্দু মানে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের কথা বলা হয় না, বর্ণহিন্দু বলতে বোঝায় শূদ্র ছাড়া বাকি সকল দ্বিজাতি। এখানে বিষয়ে উল্লেখ করা প্রয়োজন, তা হল দলিতদের উপর শুধুমাত্র বর্ণহিন্দুরাই অচ্ছুৎ বা অস্পৃশ্য ভাবে বা নির্যাতন করে, তা বললে সত্যের অপলাপ হয়। ঘৃণা নিচু জাতের সঙ্গে নিচুজাতেরও কম নেই। স্তরে স্তরে ঘৃণা। সকলেই একে অপরের থেকে উঁচু জাত সেটাই প্রমাণ করতে চায়। হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র– এই চারভাগে ভাগে ভাগ করেছে ব্রাহ্মণ্যবাদ। কিন্তু শূদ্ররা নিজেরাই বিভাজিত হয়ে আছেন হাজার ভাগে। মুচিরা মেথরদের ঘৃণা করেন, মেথররা ডোমদের ঘৃণা করেন, মণ্ডল মজুমদারদের ঘৃণা করেন, হালদাররা প্রমাণিকদের ঘৃণা করেন, বিশ্বাসরা ঘৃণা করেন বাগদিদের ইত্যাদি। অত্যাচার-নির্যাতনও চলে। একে অপরের সঙ্গে বিবাহ-শুভকার্যাদিও করেন না। উচ্চবর্ণে উন্নীত হওয়ার আকুতি অন্ত্যজদেরও বিভাজিত করে রেখেছে। উচ্চবর্ণরাই দলিতদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন করেন তা সবসময়ই নয়, অন্ত্যজরাও অন্ত্যজদের উপর অত্যাচার-নির্যাতন করেন ‘ছোটোজাতের’ অস্পৃশ্যতায়। চারখানি ঘর তো ছিলই, এই ঘরের মধ্যে ঘর তুলেছে দলিতরাও।
এ রকম হাজার হাজার ঘটনা উল্লেখ করা যায়। তাতে লাভ কী! এমন ঘটনা যেমন মায়াবতীর রাজ্যে সংঘটিত হয়, তেমনি কমিউনিস্টদের রাজ্যেও হয়। ভারতের যে-কোনো গ্রাম্য পুলিশকে তাঁর কর্তব্য সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে উত্তরে বলবে, তাঁদের কাজ ‘শান্তি রক্ষা করা। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেটি করা হয়, অবশ্যই বর্ণপ্রথাকে ধারণ করার মাধ্যমে। কারণ দলিতদের উচ্চাভিলাষই শান্তি ভঙ্গ করে। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি তার ‘নবজীবন’ নামের গুজরাটি জানালে লিখেছেন– “আমি বিশ্বাস করি যে বর্ণপ্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত বলে হিন্দুধর্ম আজও বেঁচে আছে। বর্ণপ্রথা লোপ করে পাশ্চাত্য ইউরোপিয়ান ব্যবস্থাকে গ্রহণ করা মানে হচ্ছে হিন্দুদের অবশ্যই বর্ণপ্রথার মূল ভিত্তিকে অর্থাৎ তাঁদের পূর্বপুরুষের পেশাকে ত্যাগ করতে হবে। উত্তরাধিকার সূত্র একটি চিরন্তন সূত্র। একে পরিবর্তন করা মানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। আমার কাছে একজন ব্রাহ্মণের কোনো দাম নেই যদি জীবনের মূল্যেও আমি তাঁকে ব্রাহ্মণ না ডাকতে পারি। যদি প্রতিদিন একজন ব্রাহ্মণ শূদ্রতে এবং একজন শূদ্র ব্রাহ্মণে রূপান্তরিত হয় তবে তা বিশৃঙ্খলার জন্ম দেবে।”
নমশূদ্ররা দাবি করেন বল্লালসেনের আমলেই তাঁদের সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার হরণ করে, তাদের ‘চণ্ডাল’ নামে অভিহিত করা হয়। তখন থেকেই তাঁরা হিন্দু সমাজের নিন্মতর বর্ণে অধঃপতিত হয়ে যায়। তবে ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ইংরেজ শাসনকালে আদমসুমারিতে অসন্মানজনক ‘চণ্ডাল’ নামের পরিবর্তে তাদের নতুন নাম ‘নমশূদ্র’ আনুষ্ঠানিক অনুমোদন লাভ করে। ভারতের ব্রিটিশ-মুক্তির পর চণ্ডাল তথা নমশূদ্রের নতুন পরিচয় হল ‘তফসিলি’ (তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং ওবিসি বা অনগ্রসর জাতি)।তফসিলি সৃষ্টি করে হিন্দু সমাজে তৈরি হল নতুন বর্ণবাদ। আর তাই ৭০ বছরেও শূদ্রাবস্থার অবসান হল না। তফসিলিভুক্ত সব জাতিই নিম্নবর্ণের। অর্থাৎ পূর্বে যাঁরা শূদ্র ছিলেন, আজও তাঁরা শূদ্রই আছেন। কারোর কারোর ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নতি হলেও তাঁদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তফসিলি জাতিরা [Scheduled Castes (Dalit)] কিছুটা ভালো অবস্থায় থাকলেও তফসিলি জনজাতিদের [Scheduled Tribes (Adivasi)] একদম সঙ্গিন।
কারণ সদিচ্ছার অভাব। তফসিলি জাতি ও তফসিলি জনজাতিরা সত্যি সত্যিই সাম্যবাদ সম-মর্যাদা ভোগ করুক এটা কেউ কোনোদিন মনেপ্রাণে চায়নি। ব্রিটিশ-ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব সম্ভাবনা একটা তৈরি হয়েছিল বর্ণবাদের অস্পৃশ্য সমাজব্যবস্থার জগদ্দল পাথরকে উপড়ে ফেলার। কিন্তু বাস্তবে সেই উজ্জ্বল সম্ভাবনাটাকে বাস্তবায়িত করা গেল না। কেন বাস্তবায়িত করা গেল না? ব্রিটিশ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্বে প্রায় সবাই-ই ছিলেন উচ্চবর্ণের লোক। তাঁরা কেবলই নানা পথে নানা ফন্দি-ফিকিরে নরমে-গরমে, কখনো আপোস করে কখনো পাপোস হয়ে নিজেরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতেই বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছেন। মৌলিক সামাজিক-অর্থনৈতিক কিংবা মতাদর্শগত কোনো অর্থেই পরিবর্তন ঘটানোর প্রকৃত ইচ্ছা প্রায় ছিলই না। জমিদারি স্বার্থের বিরুদ্ধে তাঁরা কখনো যেতে চাননি। বস্তুত শ্রেণিগত বিচারে যাওয়াটা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। অতএব প্রাচীন সমাজের জাতিবর্ণগত অবস্থানকে মৌলিকভাবে পরিবর্তনের কোনো কর্মসূচি কোনোদিনই জাতীয় আন্দোলনে নেওয়া হয়নি। জাতীয় আন্দোলনে ক্রমবর্ধমান জোয়ারে নিচুবর্ণের মানুষেরা প্রচুর সংখ্যায় এলেও জাতিবর্ণগত বিভেদের মূল উৎপাটনে জাতীয় নেতৃত্বের অনীহা ও বাস্তব সক্রিয়তার অভাব অনেক সময়েই তাঁদের দূরে সরিয়ে দিয়েছে। দূরে সরিয়ে দিলেই কি দূরে সরানো যায়! শূদ্ৰজাতিদের যতই এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে জাতীয় নেতৃত্বে শূদ্রেরা ততই সংঘবদ্ধ হয়েছে। ততই প্রকটিত হয়েছে।
আমাদের এই ভারত উপমহাদেশে প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত বারবার বিদেশি আক্রমণকারীরা আক্রমণ করেছে, দখল করেছে, শাসন করেছে। কীভাবে পারল? পারল কারণ ভারতীয়রা হাজার খণ্ডে খণ্ডিত। এক খণ্ডিত জাতিকে কুপোকাত করা তো অখণ্ড জাতিদের কাছে বাঁয়ে হাথ কা খেল। তাই খণ্ডিত জাতিদের কাছ থেকে কোনো প্রতিরোধ আসেনি। তাই অবলীলায় নিজেদের পরহস্তগত হয়ে গেছে বারবার। হাজার হাজার ধরে ভারতীয়রা পরাধীন থেকে গেছে। গোটা উপমহাদেশে ব্রাহ্মণরাই রাজ করবে, অথচ রাজত্ব রক্ষা করতে পারেনি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী শূদ্রদের বিচ্ছিন্ন করে রেখে। শূদ্রদের প্রতি ঘৃণা সনাতন ধর্ম দুর্বল থেকে দুবর্লতর হয়ে গেছে। যে মন্দিরে শূদ্রদের প্রবেশাধিকার দেওয়া হত না, সেই মন্দির কেন শূদ্ররা রক্ষা করবে? যে মন্দির শূদ্রদের নয়, যে মন্দিরে ব্রাহ্মণদেরই একাধিপত্য, যে মন্দিরে ঢোকার অপরাধে শূদ্রদের হত্যা করা হয়েছে, সেই মন্দির কেন তাঁরা রক্ষা করবে? ওই মন্দিরের দেবতা তো কোনোদিনই শূদ্রদের ছিল না। সেই কারণে সুলতান মামুদের পক্ষে ১৭ বার সোমনাথমন্দির লুঠপাট করতে, ধ্বংস করতে। শুধু তো সোমনাথ মন্দিরই নয়, খাজুরাহো মন্দির ধ্বংস হয়েছে প্রতিরোধে। এই দেশ তো বৌদ্ধদেরও ছিল। তাঁদের উপরেও অত্যাচার করে দেশ থেকেই বিতারণ করে দিয়েছে ব্রাহ্মণবাদীরা। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অত্যচার আর বঞ্চনায় নিম্নবর্গীয়রা সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম বা অন্যান্য ধর্ম গ্রহণ করেছে। সনাতন ধর্মের জাতিরা ক্রমশই শক্তিহীন হয়ে পড়ল। আজও হারানো শক্তি অর্জন করতে পারছে না বিভাজনের কারণে। সেই ট্র্যাডিশন আজও চলিতেছে। সমগ্র হিন্দু জাতিকে জাগানো যাচ্ছে না। শতধায় বিভক্ত একটা জাতি সদাসর্বদা আত্মহননে ব্যস্ত। আজও দলিত তথা শূদ্র জাতিদের ঘৃণার চোখে দেখা হয়, অমানবিক অত্যাচার করা হয়।
তাই কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছে করছে— “যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে, সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তাঁরে;/যে জাতি জীবনহারা অচল অসার, পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাঁচার”
১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ। সেদিন ছিল বড়োদিন। বাবাসাহেব ডাক দিলেন মহারদের সহ অন্যান্য দলিতদের –“এসো, আমরা ওই নিষিদ্ধ জলে স্নান করি, ওই নিষিদ্ধ জল পান করি।” ‘নিষিদ্ধ জল’ কেন! যুগ যুগ ধরে চাদর সরোবরের জল স্পর্শও করতে পারত না দলিতরা। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের এটাই নিষেধাজ্ঞা। সেই সরোবরের জল বৰ্ণহিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান-কুকুর-গোরু-মোষ-গাধা কারোরই জন্য নিষেধ ছিল না, বাদ ছিল দলিতরাই। যাই হোক, বাবাসাহেবের ডাকে সেই সরোবরে জমায়েত হলেন হাজার হাজার দলিত মানুষ। বিশাল এক সমাবেশ হল। উচ্চবর্ণদের সাহসে কুলালো না একজন দলিতের মাথা ডাণ্ডা মেরে ঠান্ডা করার। পুলিশ পুতুল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অকুস্থলে। হাজার হাজার দলিত মানুষ সেই সরোবরের জলে নেমে পড়লেন। শিশুদের মতো জলে নেমে স্নান করতে থাকলেন এবং নাচতে থাকলেন। সরোবরের পাড়েই আয়োজিত হল বিরাট জনসভা। পুড়িয়ে দেওয়া হল সেই গ্রন্থ, যে গ্রন্থ সংখ্যাগরিষ্ঠ শূদ্রদের ঘৃণ্য করেছে। হ্যাঁ, মনুসংহিতা। সেইদিন থেকে এমন গ্রন্থ সমাজ থেকে নিষিদ্ধ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু সেটা হয়নি। উচ্চবর্ণের উচ্চাসন টলে যাবে যে!
১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন– “সকল জাতিকেই আমাদের জলচল করিয়া লইতে হবে।” কীভাবে জলচল করে নেওয়া যাবে যতদিন মনুসংহিতার প্রভাব থাকবে? ভারতের সেকুলার শাসনকর্তারা ভারতের অস্পৃশ্য-অচ্ছুৎদের জলচল করে তোলার শিক্ষা দিতে ভয় পায়, নিতেও। কারণ হিন্দুত্বকে ধ্বংস না করে নিম্নবর্গদের জলচল করা সম্ভব নয়। তাই বোধহয় দলিতদের শ্লোগান এমনই হয়ে যায় –“তিলক, তরাজু অওর তলোয়ার ইনকো মারো জুতে চার”। ব্রাহ্মণের তিলক, ক্ষত্রিয়ের তলোয়ার এবং বেনিয়ার তরাজু (দাঁড়িপাল্লা)। উত্তরপ্রদেশের ‘চামার কি বেটি’ মায়াবতী মুখে দলিতদের কথা বললেও ব্রাহ্মণরা স্বাগত ছিলেন। তাঁর কাছে বেনিয়া-ক্ষত্রিয়রা অচ্ছুৎ হলেও, ব্রাহ্মণরা নন। ক্ষমতার রাজনীতি বড়ো বালাই, সত্যি! অথচ মনুবাদের যথার্থ এবং প্রবলতম প্রবর্তক এই ব্রাহ্মণরাই। কারণ কী? বর্ণযোদ্ধাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা? হ্যাঁ, ভারতের প্রথম বর্ণযযাদ্ধাই পরশুরাম, যিনি ব্রাহ্মণ। একবার নয়, একুশবার ধরিত্রীকে নিঃক্ষত্রিয় করার যুদ্ধ করেছেন। ব্রাহ্মণ বনাম ক্ষত্রিয়ের যে দ্বন্দ্ব একদা আর্য ও দ্রাবিড়ভূমিকে দীর্ণ করেছিল, ব্রাহ্মণদের তরফে পরশুরামই ক্ষত্রিয় হৈহয় অধিপতি কার্তবীর্যাজুনকে সপরিবার নিধন করে তার শীর্ষবিন্দু রচনা করেন। এমন বর্ণযোদ্ধাকে ‘দেবী’ মায়াবতী আর কোথায় পাবেন? সেই কারণেই কাঁসিরামের মানসপ্রতিমা মায়াবতীকে উত্তরপ্রদেশের জেলার জেলায় ব্রাহ্মণ সম্মেলন করে বেড়াতে দেখা যায়। সেই ব্রাহ্মণ সম্মেলনের মঞ্চে দেখা যায় একদিকে একটি বাবাসাহেব আম্বেদকর, অন্য একটি পরশুরামের মাল্যবান কাট-আউট।
একটা বড়ো প্রশ্ন –তা হল উচ্চবর্ণের সর্বোচ্চ আসনে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণরা কেন ঘৃণ্য ‘চামার কি বেটি’ মায়াবতীর বহুজন সমাজের হাতি চিহ্ন-সংবলিত পতাকার নীচে আশ্রয় নিল? আসলে উত্তরপ্রদেশে সৃষ্ট হওয়া গড্ডলিকা প্রবাহ। এখানে দলিতদের সংগঠন আছে, জনজাতিদের সংগঠন আছে, অনগ্রসরদেরও সংগঠন আছে –ব্রাহ্মণদের কোনো সংগঠন নেই। তার মানে কী ব্রাহ্মণ্যবাদী আর্যাবর্তের দলিতায়ন থেকে দলিতের ক্ষমতায়নের রূপান্তর!
ভারতীয় সংবিধান ভারতের অনগ্রসর জনসমষ্টিকে তিনভাগে ভাগ করেছে— (১) তফসিলি জাতি (Scheduled Caste বা S.C), (২) তফসিলি উপজাতি (Scheduled Tribes বা S.T.) এবং (৩) অন্যান্য অনগ্রসর জাতিসমূহ (Other backward Classes বা 0.B.C.)। ভারত সরকার সংবিধানের ৩৪০ ধারা অনুযায়ী ভারতের অনগ্রসর শ্রেণিগুলির সমস্যাদির অনুসন্ধান এবং তা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার সুপারিশ গ্রহণের জন্য এ পর্যন্ত দুটি কমিশন নিযুক্ত হয়েছে। ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে কাকা কালেলকার কমিশন এবং ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে মণ্ডল কমিশন। লক্ষণীয় যে, সংবিধান তফসিলি জাতি বা উপজাতিদের তালিকা নির্ণয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিনির্ধারণ করলেও অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়গুলির ক্ষেত্রে তেমন কিছু করেনি। কেবল বলা হয়েছে, যে আদেশবলে কমিশন নিযুক্ত হবে সেই আদেশেই কমিশনের কার্যপদ্ধতি বিবৃত থাকবে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় প্রতিটি ব্যক্তি বা সম্প্রদায়েরই সংগত অধিকার ও আকাঙ্ক্ষা থাকে দেশের শাসন-প্রশাসনে অংশগ্রহণ করার। যে পরিস্থিতি দেশের ৫২%। জনগণকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করে, অবশ্যই তার জরুরি সংশোধন প্রয়োজন।
ভারত স্বাধীনতা অর্জনের পর যে নতুন সংবিধান গৃহীত হল তাতে ন্যায়, স্বাধীনতা এবং সমতার প্রতিশ্রুতি রক্ষার কথা বলা হল। বলা হল আইনের চোখে সব নাগরিকই সমান এবং ১৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী আইন তাঁদের এই অধিকার রক্ষা করবে। ১৫ এবং ১৬ নম্বর ধারা মোতাবেক কারও প্রতি বৈষম্য–করার নীতি গৃহীত হল। ১৭ নম্বর ধারা মোতাবেক অস্পৃশ্যতার মতো ঘৃণ্য প্রথা নিষিদ্ধ করা হল। পাশাপাশি সংবিধান সামাজিকভাবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলোকে বিশেষ সহায়তাকে স্বীকৃতি দেয়। কিছু পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীকে ক্ষতিপূরণমূলক বৈষম্যের সুযোগ দেওয়া হয়। প্রেসিডেন্টের ১৯ নম্বর সাংবিধানিক আদেশে (তফসিলি জাতি) যেসব জাতিকে তফসিলি জাতি বলে গণ্য করা হবে তার তালিকা দেওয়া হয়। শুধু হিন্দুরাই নয়, শিখ-বৌদ্ধরাও তফসিলি জাতিভুক্ত। পূর্বে যাঁদের অস্পৃশ্য জাতি বলা হত তাঁরাই স্বাধীনোত্তর ভারতে তফসিলি। এদের সুযোগ-সুবিধার কথা বলা আছে তা মূলত তিন প্রকারের। প্রথমতঃ, এই জনগোষ্ঠীর সদস্যদের আইনসভায়, সরকার-চালিত বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণ। দ্বিতীয়তঃ ঋণ, স্কলারশিপ, জমির পাট্টা ইত্যাদি নানাবিধ আর্থিক সুবিধা। তৃতীয়তঃ অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে নানাবিধ ব্যবস্থা এবং আবদ্ধ শ্রমিকদের মুক্ত করার কিছু পদক্ষেপ। বাস্তবে ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে আধিপত্য ছিল ইংরেজি জানা শহুরে রাজনৈতিক নেতাদের। বস্তুত রাজ্য ও স্থানীয় স্তরে উচ্চবর্ণের এবং অন্তত উত্তর ভারতে এঁরা ছিলেন উচ্চবর্ণ জমি মালিক শ্রেণির। দক্ষিণ ভারতে পরিস্থিতি কিছুটা আলাদা ছিল। কারণ পঞ্চাশের দশকের মধ্যেই নিম্নবর্ণ নেতারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ঢুকতে শুরু করেছিলেন। ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে তামিলনাড়তে দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজাঘাম ক্ষমতায় আসে। এটা ছিল একটি অ-ব্রাহ্মণ পার্টি। ৫০/৬০ দশকে দক্ষিণ ভারতের নিন্মবর্ণগুলি নিজেদের পার্টি ও নেতা তৈরি করে ফেলেছিল। ৮০ এবং ৯০-এর দশকে উত্তর ভারতেও নিম্নবর্ণ রাজনৈতিক উত্থান শুরু হয়ে যায়। বারংবার লালুপ্রসাদ যাদব, কাঁসিরাম এবং মায়াবতীর নাম সামনে আসতে থাকে। ১৯৮৯ থেকে ১৯৯১ এবং আবার ১৯৯৬ থেকে ১৯৯৮ মূলত নিম্নবর্ণ রাজনৈতিক জোট দিল্লির ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে।
১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে অখণ্ড ভারত খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল রাজনৈতিক কুটিলতায়। ঘরছাড়া হয়ে ভেসে গেল লক্ষ লক্ষ মানুষ, এঁদের মধ্য একটা বড় অংশই ছিল দলিত শ্রেণি। ১৯৪৭, ১৯৪৯-এর পর ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে সরকারি হিসাব অনুযায়ী আসাম-ত্রিপুরা-পশ্চিমবঙ্গ মিলিয়ে পনেরো লক্ষ বিরাশি হাজার উদ্বাস্তু ভারতে চলে আসে। এদের মধ্যে প্রায় ১৬ আনাই ছিল দলিত শ্রেণি এবং বেশিরভাগই নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মানুষ। ভারতে ফেরার পর এঁদের অবস্থা মোটেই ভালো হয়নি, আজও। সংসদীয় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান চালু হতেই যে জাতিগত বৈষম্য ও নিপীড়ন শেষ হয়ে গেল তা বলা যায় না। তবে পূর্বে যেমন সমস্ত রকমের নিপীড়ন মুখ বুজে সহ্য করে যেত, এখন তেমন নয়। প্রতিবাদ করতে শিখেছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় আন্দোলিত হতে থাকল শূদ্র জাগরণের তরঙ্গ। নিচুজাতির মানুষেরা নিজেদের দাবি উত্থাপন করার এবং জাতিব্যবস্থাকে বিরোধিতা করার আন্দোলন ক্রমশ জঙ্গিরূপ গ্রহণ করতে থাকে। মন্দিরে ঢোকা, পুকুর-কুয়ো-রাস্তা ব্যবহারের আন্দোলনের মধ্যে এটা লক্ষ করা যায়। ব্রাহ্মণ্যবাদী ব্যবস্থার বিরোধিতা শুধু অস্পৃশ্য জাতিগুলি করেনি, যাঁরা অস্পৃশ্য ছিল না সেই শূদ্র জাতিগুলিও সামনে এগিয়ে আসতে থাকে। দক্ষিণ ভারতে ই ভি রামস্বামীর নেতৃত্বে এই শূদ্র প্রতিবাদ সুসংহত রূপ ধারণ করে। সংগঠিত হল এবং বিপ্লবী রূপ গ্রহণ করল। তিনি তামিলনাড়ুর অব্রাহ্মণদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতার জন্য ব্রাহ্মণদের এবং তাঁদের সংস্কৃতভিত্তিক ভাবধারাকে দায়ী করে। তিনি সেই সংস্কৃতির শিকড় সমূলে উৎপাটন করতে চেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, যেসব বিষয়ে ই ভি রামস্বামীর নেতৃত্বাধীন ‘আত্মসম্মান’ আন্দোলন লাগাতার সংগ্রাম গড়ে তোলে সেগুলি হল মন্দিরে প্রবেশ, সমস্ত সরকারি প্রতিষ্ঠানে এবং রাস্তায় প্রবেশের অধিকার, অস্পৃশ্যতা বর্জন, তদুপরি ব্রাহ্মণ্যবাদ-জাতিব্যবস্থা-ধর্মের বিরোধিতা করা। এই আত্মসম্মানপন্থীরা ছিলেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত ও ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী, ধর্মশাস্ত্র বিরোধী এবং ধর্মীয় বিশ্বদৃষ্টিকোণ ও রীতিনীতির বিরোধী তথা ধর্মীয় উৎসবের বিরোধী।
সবই আছে, কিন্তু প্রয়োগ কোথায়? সুরক্ষা আছে, সুরক্ষার কবচও আছে– কার বাজুতে বাঁধা আছে সেই কবচ? কেমন সেই কবচ? একনজরে দেখে নিতে পারি সকলের অবগতের জন্য। তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতিদের উপর তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি নয় এমন কেউ যে যে নিপীড়ন চালানোর অপরাধে যেরকম শাস্তির বিধান আছে, সেগুলি হল– (১) যদি তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত কোনো ব্যক্তিকে কোনো অখাদ্য বা অপেয় বস্তু খেতে বা পান করতে বাধ্য করলে, (২) যদি তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত কোনো মানুষের বাড়ির উঠোনে বা আশেপাশে মলমূত্র, বর্জ্য পদার্থ, মরা পশু বা অন্যান্য আপত্তিকর বস্তু নিক্ষেপ করলে এবং এইভাবে সেই ব্যক্তিকে আহত, অপমানিত বিরক্ত করলে, (৩) যদি তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত কোনো মানুষের শরীর থেকে কাপড় খুলে নিলে, বা তাকে নগ্ন করে হাঁটায়, বা তাঁর মুখে রং মাখিয়ে হাঁটায় বা এই ধরনের মানবিক মর্যাদা হানিকর অপর কোনো কাজ করলে, (৪) যদি তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত কোনো ব্যক্তির মালিকাধীন বা যথাসাধ্য কর্তৃপক্ষ তাঁকে যে জমি চাষ করার জন্য দিয়েছে সেই জমি অন্যায়ভাবে দখল করার চেষ্টা করলে বা সেই জমি হস্তান্তরিত করে নিলে, (৫) যদি তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত কোনো ব্যক্তিকে তাঁর জমি বা বাসস্থান থেকে উচ্ছেদ করলে অথবা জমি, বাসস্থান বা জলের উপর যে অধিকার সে ভোগ করছে তা থেকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করলে, (৬) যদি তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত কোনো মানুষকে ‘বেগার’ বা অন্য কোনো ধরনের বাধ্যতামূলক শ্রম করতে বাধ্য করলে, (৭) যদি তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত কোনো ব্যক্তিকে নির্বাচনে কোনো প্রার্থীকে ভোট দিতে বা না দিতে বাধ্য করলে অথবা আইনানুগ নয় এমনভাবে ভোট দিতে বাধ্য করলে, (৮) যদি তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত কোনো ব্যক্তির নামে মিথ্যা বা উদ্দেশ্যমূলক মামলা করলে, (৯) কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষের কাছে এমন কোনো তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা বা সাজানো অভিযোগ করে যার ভিত্তিতে ওই সরকারি ব্যক্তি সেই তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষটির কোনো ক্ষতি বা তাকে বিরক্ত করলে, (১০) প্রকাশ্য স্থানে কোনো তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি ভুক্ত মানুষকে ইচ্ছাকৃতভাবে অপমান করে বা ভয় দেখায়, (১১) কোনো তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলাকে অসম্মান বা শ্লীলতাহানির জন্য ভয় দেখালে, (১২) নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করে কোনো তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মহিলার উপর যৌনশোষণ চালায় (এই ক্ষমতা না থাকলে মহিলাটি যৌনক্রিয়ায় রাজি হবে না), (১৩) তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্তদের ব্যবহার্য পুকুর, কুয়ো বা খালের জল দূষিত করলে এবং সেটাকে ব্যবহারের অযোগ্য করলে, (১৪) সর্বসাধারণের ব্যবহার্য যেসব স্থান অন্যরা ব্যবহার করে এবং তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতিদের সেগুলি ব্যবহার করতে বাধা দিলে, (১৫) কোনো তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি মানুষকে গ্রাম বা তার বাসস্থান ছাড়তে বাধ্য করলে– এইসব অপরাধের জন্য অপরাধীর ন্যূনতম ছয়মাস এবং সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড ও জরিমানা হতে পারে।
এখানেই শেষ নয়, যদি (১) তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি নয় এমন কেউ তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতি মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় (এটা জেনে যে ওই সাক্ষ্যের ফলে তার মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে), তাহলে এই অপরাধের জন্য তাঁর যাবজ্জীবন সাজা এবং জরিমানা হতে পারে; এবং যদি এই ধরনের সাক্ষ্যের ফলে কোনো তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতির তালিকাভুক্ত ব্যক্তির সাজা ও মৃত্যুদণ্ড হয়ে যায় তাহলে মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী ব্যক্তির সাজা মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে। (২) যদি অগ্নিসংযোগ করে বা বিস্ফোরক ফাটায় (এটা জেনে যে তাতে তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতির মানুষদের সম্পত্তির ক্ষতি হতে পারে) তাহলে ওই ব্যক্তির সর্বনিম্ন ছয়মাস সাজা হতে পারে বা সর্বোচ্চ সাত বছর কারাদণ্ড ও জরিমানা হতে পারে।
রাষ্ট্রের কাছে গচ্ছিত আছে আপনাদের রক্ষাকবচ, আর আপনাদের কমণ্ডলুতে আছে ব্রাহ্মণ্যবাদের রক্ষাকবচ। ছুঁড়ে ফেলে দিন। একদা যে ব্রাহ্মণ্যবাদকে ঘিরে হিন্দুধর্ম পরিপূর্ণতা এবং পরিপুষ্টতা লাভ করেছিল, সেই ব্রাহ্মণ্যবাদের কারণেই হিন্দুধর্ম ক্ষয়িষ্ণুর পথে। ব্রাহ্মণ্যবাদই হিন্দুধর্মের আধার। এই ব্রাহ্মণ্যবাদ ধ্বংস না-হলে হিন্দুধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে কালের স্রোতে। বহু বিভাজনে কোনো জাতি টিকে থাকতে পারে না। যতদিন না এক মন এক মত এক জাতি এক ধর্ম হবে ততদিন বিচ্ছিন্ন হতে হতে একটা জাতি অক্ষমের লড়াই করতে থাকবে আরএসএসের হাত ধরে। আক্ষেপের বিষয় হল এই যে, ব্রাহ্মণ্যবাদ যত-না মুষ্ঠিমেয় উচ্চবর্ণীয়রা অনুসরণ করে তার চেয়ে অনুসরণ করে তথাকথিত নিম্নবর্ণীয় বৃহৎ সংখ্যক মানুষেরা। অথচ বিবেকানন্দ থেকে জগজীবন রাম প্রত্যেকেই পইপই করে বলেছেন– ব্রাহ্মণ্যবাদ ধ্বংস করো, পুরোহিততন্ত্রের বিনাশ করো। শুধু আমরা দলিত আমরা দলিত’ বলে চিৎকার করলে কিস্যু হবে না, ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ্যবাদগুলি ইগনোর করতে হবে। সেইজন্যই জগজীবন রামের কথা স্মর্তব্য– “Any movement for social equaliy must be anti-Brahmin in character.” অর্থাৎ সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য যদি কোনো আন্দোলন গড়ে তুলতে হয় তবে তা হতে হবে ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী। “হিন্দুধর্মের যথার্থ নাম ব্রাহ্মণ্যবাদ, আর হিন্দুধর্ম হল প্রকৃতপক্ষে জাতব্যবস্থা। ব্রাহ্মণ্যবাদ ধ্বংস নাহলে ভারতে সমাজতন্ত্র আসতে পারে না (“Brahminism, which is the appropriate name for Hinduism, is nothing but Cast System. Socialism will not come to India without destroying Brahminsim”– V.T. Rajshekhar) i
ইগনোর করুন ব্রাহ্মণ্য-ব্যবস্থা। কীভাবে ইগনোর করবেন? শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে ব্রাহ্মণদের নির্দেশ হলে এমন সব নির্দেশ অগ্রাহ্য করুন। কারণ তথাকথিত শাস্ত্র যা, শাস্ত্রের লিখন যা –তার সবই ব্রাহ্মণ-শাসক দ্বারা রচিত। যেমন– মন্ত্রপাঠ করে বিয়ে করা (রেজিস্ট্রি করে ম্যারেজ করুন, সামর্থ্য অনুযায়ী প্রীতিভোজ দিন)। শিশু প্রথম ভাত খাক এবং তা মামাই খাওয়াক (পুরোহিত আনবেন না), প্রীতিভোজও সামর্থ্য অনুযায়ী। পুজো করতে চাইলে আপনি নিজে করুন, পুরোহিতের প্রয়োজন নেই, মন্ত্রও লাগে না। প্রিয়জন বিয়োগে মৃতদেহ দাহ করুন বা মাটি দেন– এখানেই সৎকার শেষ করুন। হবিষ্যি খাওয়া, অশৌচ পালন, ধরা বাঁধা, মস্তক মুণ্ডনাদি ক্ষৌরকর্ম, পিণ্ডদান, ব্রাহ্মণভোজন, প্রীতিভোজ বাতিল করুন। সবচেয়ে উত্তম হয় যদি আপনার আত্মীয়ের মরদেহ মেডিক্যালে বিজ্ঞানের স্বার্থে দান করতে পারেন। উত্তম এই কারণে যে, মানুষের মৃত্যুর পর মরণোত্তর দেহদানের পর কী করণীয় তার কোনো শাস্ত্রীয় অঙ্গুলি-নির্দেশ বা বিধান নেই। তাই কোনো চাপও থাকছে না। অ-কার্যকর সংরক্ষণ ব্যবস্থার বিরোধিতা করুন, এ ব্যবস্থা আপনার কোনো কাজে লাগে না। এ ব্যবস্থা আপনাকে ভয়ানকভাবে চিহ্নিত করে যে, আপনি দুর্বল, অযোগ্য, আপনি ছোটোজাত, আপনি পরাজিতের দলে, আপনি অসুর দৈত্য-দানো। যোগ্যতার মাপকাঠিতে সমস্ত ক্ষমতা অর্জন করতে হবে, মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে হবে, নইলে নয়। দয়া নয়, অর্জন করে নিতে হবে। আপনারা সংখ্যালঘু নন, আপনারাই সংখ্যাগুরু।
————
সাহায্যকারী তথ্যসূত্র :
১. ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস –নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
২. বৌদ্ধ দর্শন– রাহুল সাংকৃত্যায়ন
৩. অলৌকিক নয় লৌকিক (তৃতীয় খণ্ড)– প্রবীর ঘোষ
৪. মুসলিম সমাজ কয়েকটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা— মইনুল হাসান
৫. বাংলার সমাজে ইসলাম সুচনাপর্ব– অতীশ দাশগুপ্ত
৬. ব্রাহ্মণ্যবাদ– রণজিৎ কুমার সিকদার
৭, অনীক(অক্টোবর-নভেম্বর ২০০৫)
৮. আমি শূদ্র, আমি মন্ত্রহীন– কঙ্কর সিংহ
৯. মনুসংহিতা– সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
১০, ক্ষমতা হস্তান্তর ও দেশবিভাগ– লাডলীমোহন রায়চৌধুরী
১১. অনীক (অক্টোবর-নভেম্বর ২০০৫)।
১২. মানবাধিকার ও দলিত– দেৰী চ্যাটার্জী,
১৩. শূদ্র জাগরণ– গৌতম রায়,
১৪. বর্তমান ভারত– স্বামী বিবেকানন্দ,
১৫. প্রাচীন ভারতে শূদ্র– রামশরণ শর্মা,
১৬. জাতের বিড়ম্বনা– শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
মৃত্যুদণ্ড : রাষ্ট্র কর্তৃক নরমেধ যজ্ঞ
মৃত্যুদণ্ড বা প্রাণদণ্ড (Capital Punishment) হল আইনি পদ্ধতিতে কোনো ব্যক্তিকে শাস্তিস্বরূপ হত্যা করা। যেসব অপরাধের শাস্তি হিসাবে সাধারণত মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়ে থাকে, সেগুলিকে বলা হয় মৃত্যুদণ্ডাই অপরাধ। অতীতে প্রায় সকল দেশেই মৃত্যুদণ্ড প্রথা প্রচলিত ছিল। বর্তমানে মাত্র ৫৮টি দেশ প্রত্যক্ষভাবে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে থাকে। ৯৫টি দেশ এই প্রথা অবলুপ্ত করে দিচ্ছে। অবশিষ্ট দেশগুলি ১০ বছর এই দণ্ড ব্যবহার করছে না বা যুদ্ধ ইত্যাদি ব্যতিক্রমী ঘটনা ছাড়া মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগ করছে না। অনেক দেশেই মৃত্যুদণ্ড একটি বিতর্কের বিষয়। তবে একই রাজনৈতিক আদর্শ ও সাংস্কৃতিক অঞ্চলে মৃত্যুদণ্ড নিয়ে মতান্তর রয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মৌলিক অধিকার সনদের ২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভুক্ত দেশগুলির উপর মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।
অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল অধিকাংশ দেশকেই ‘অ্যাবোলিশনিস্ট’ অর্থাৎ মৃত্যুদণ্ড বিলোপের পক্ষপাতী মনে করে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল মৃত্যুদণ্ড বিলোপের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসংঘে একটি অবাধ্যতামূলক প্রস্তাবনায় ভোটের অনুমোদন দিয়েছে। যদিও বিশ্বের ৬০ শতাংশ মানুষ সেই সব দেশে বাস করেন, যেখানে মৃত্যুদণ্ড প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে রয়েছে বিশ্বের সর্বাধিক জনসংখ্যাবিশিষ্ট চারটি দেশও (গণচিন, ভারত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইন্দোনেশিয়া)। চারটি দেশই ২০০৮ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় Resolution on a moratorium on the use of the death penalty’ এর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। আসলে রাষ্ট্র তখনই সেই ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেবে, যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের পক্ষে ঝুঁকিকর হতে পারে। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সেই মৃত্যুদণ্ডই কাক্ষিত, যদি কোনো ব্যক্তি বিদ্রোহী হয়– এই বিদ্রোহীদেরই ‘রাষ্ট্রদ্রোহী’ হিসাবেই প্রতিপন্ন করা হয় এবং মৃত্যুদণ্ডপূর্বক হত্যা করা হয়।
মৃত্যুদণ্ড হল অপরাধীর জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি। যদিও পৃথিবীর অনেক দেশ আছে, যেখানে সর্বোচ্চ শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না। কিন্তু বিশ্বের বেশিরভাগ দেশে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিধি আছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পদ্ধতি একেক সময়ে একেক পদ্ধতিতে দেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছেও। আমি এখানে মৃত্যুদণ্ডের ৩৬টি পদ্ধতি উল্লেখ করব। যদিও সবকটি পদ্ধতি এখন আর কার্যকর হয় না, তবুও জেনে রাখব।
(১) ইলেকট্রিক চেয়ার : মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিটিকে একটা চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে বসিয়ে দেওয়া হয়। এরপর সেই ব্যক্তির মাথায় একটা ভেজা স্পঞ্জ লাগানো হয়, যাতে বিদ্যুৎপ্রবাহ সহজেই কার্যকর হতে পারে। তার মাথায় এবং পায়ে ইলেকট্রোড লাগিয়ে দেওয়া হয়। সাধারণত দু-বার বিদ্যুৎপ্রবাহ তাঁর শরীরের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করানো করা হয়। প্রথমবার ২০ সেকেন্ডের জন্য ২০০০ ভোল্ট বিদ্যুৎ। এর ফলে ব্যক্তিটির হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে যায়। এরপর দ্বিতীয়বারের বিদ্যুৎপ্রবাহের ফলে তার শরীরের ভিতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুড়ে যায়।
(২) গ্যাস চেম্বার : একটি চেম্বারে ছোটো একটা এয়ার-টাইট চেয়ার রাখা হয়। যাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে তাঁকে এই চেয়ারে বসিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। চেয়ারের নীচে একটা পাত্রে পটাশিয়াম সায়ানাইড ক্যাপসুল রেখে বাইরে থেকে চেম্বার বন্ধ করে দেওয়া হয়। এরপর একটা নলের সাহায্যে বাইরে থেকেই চেয়ারের নীচে রাখা আর-একটি পাত্রে সালফিউরিক অ্যাসিড ঢেলে দেওয়া হয়। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি তখন তাঁর শেষ কথা বলে বা ইচ্ছা প্রকাশ করে। এরপরই মেসিনের সাহায্যে সায়ানাইড ক্যাপসুল এবং অ্যাসিড একসঙ্গে মেশানো হয়। এর ফলে চেম্বার পটাশিয়াম সায়ানাইড গ্যাসে ভরে যায়। যাতে মৃত্যু ত্বরান্বিত হয় সেইজন্য মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ঘনঘন শ্বাস নিতে বলা হয়। ঘনঘন শ্বাস নেওয়ার ফলে শরীরে তাড়াতাড়ি গ্যাস প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তবে অনেকক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি মৃত্যুভয়ে শ্বাস আটকে রাখে বলে মৃত্যু বিলম্বিত হয়ে যায়।
(৩) ফায়ারিং স্কোয়াড : মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির চোখ এবং হাত বেঁধে একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা হয়। এরপর তাঁর বুকে গোল একটা টার্গেট পেপার ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। কিছুটা দূরে পাঁচ-পাঁচজন শুটার দাঁড়িয়ে থাকে। এদের প্রত্যেককে একটা করে গুলি দেওয়া হয়। পাঁচজনের মধ্যে চারজনের কাছে আসল গুলি থাকে না, থাকে ব্ল্যাংক গুলি। কিন্ত কোন্ চারজনের কাছে ব্ল্যাংক গুলি আছে সেটা পাঁচজন শুটারের একজনও জানতে পারবে না। কারণ ওদের কেউই বুঝতে পারবে না ঠিক কার গুলিতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ‘ফায়ার’— হুকুম বা নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে পাঁচজন শ্যটারই একসঙ্গে গুলি করে এবং মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যু হয়। তবে কোনো শ্যটার যদি গুলি না-করে তাহলে তাঁর জন্য থাকে শাস্তির ব্যবস্থা।
(৪) ফাঁসি : আইনানুগ সকল ফর্মালিটি শেষে ফাঁসির মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে যেখানে নিয়ে আসা হয় সেটাকে বলে কনডেম সেল’। সেখানে শুধু ফাঁসির আসামীদেরই রাখা হয়। বিভীষিকাময় সেই সেল অনেকটা ওয়েটিং রুমের মতো হলেও আসামীকে একাই দিন গুজরান করতে হয়। যতদিন ফাঁসি কার্যকর না হয়, ততদিন নরক-যন্ত্রণা। না মরেও মৃত্যু-যন্ত্রণা। যে কদিনের জন্য তাঁকে রাখা হয়, তাঁর সঙ্গে যথাসম্ভব ভালো ব্যবহার করা হয়।
ফাঁসির জন্য বিদেশ থেকে আনা হয় দড়ি। সাধারণত জার্মানি থেকে বিশেষ এই দড়ি আনা হয়। নিয়ম করে কয়েকবার এতে মাখানো হয় সবরি কলা আর মাখন। জল্লাদ নির্বাচন করা হয় কয়েদিদের মধ্য থেকেই অথবা পেশাদার জল্লাদ। কোনো কোনো দেশে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদিদের দিয়ে ফাঁসি কার্যকর করালে প্রতিটি ফাঁসি কার্যকরের জন্য ওই কয়েদির ২ মাস করে সাজা কমে যায়। আসামীর সম-ওজনের বালির বস্তা দিয়ে কয়েকদিন আগে থেকেই ফাঁসি দেওয়া প্র্যাকটিস করে নিতে হয়। কনডেম সেলে আসামীর আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করানো হয়। তবে অনেকক্ষেত্রেই কবে ফাঁসি কার্যকর হবে তা আসামী এবং আত্মীয়স্বজন কাউকেই বুঝতে দেওয়া হয় না। কিন্তু ফাঁসির দিন কয়েদি বুঝতে পারেন যে আজই তাঁর জীবনের শেষ রাত। দণ্ডপ্রাপ্তের কালো কাপড় মাথা ঢেকে দেওয়া হয় এবং গলায় দড়ি পরিয়ে দেওয়া হয়। জেল সুপার হাতে রুমাল নিয়ে ফাঁসির মঞ্চের পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। দাঁড়িয়ে থাকেন চিকিৎসকসহ আরও কয়েকজন। জল্লাদের চোখ তখন রুমালের দিকে। ওই মুহূর্তে এই রুমালই একজন মানুষকে এ-পার থেকে ও-পারে পাঠিয়ে দেওয়ার ভূমিকা পালন করে। রুমালের হেলনে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির পায়ের নিচ থেকে পাটাতন সরে যায়। গলায় আটকে যায় মোটা দড়ি। ১০ মিনিট ঝুলিয়ে রাখার পর একজন ডাক্তার এসে ঘাড়ের চামড়া কেটে মৃত্যু নিশ্চিত করেন। পড়ে থাকে নিথর দেহ। ফাঁসির দৃশ্য সাধারণত ভিডিও করা হয় না। তবে ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মান ও জাপানি যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসি ভিডিওতে ধারণ করেছিল। জার্মানির নুরেমবার্গ ট্রায়ালের সেই ভিডিওটি ইউটিউব ঘাঁটলেই দেখতে পাবেন। প্রায় ৬৫ বছর আগের ভিডিও, যেটা ২৮ মে ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দে কার্যকর করা হয়েছিল ল্যান্ডসবার্গ জেলে। সংক্ষিপ্ত সময়ের ট্রাইবুন্যালের রায়ের কোনো আপিল করার সুযোগ দেওয়া হয়নি।
(৫) অন্য ফাঁসি, জলে ডুবানো এবং খণ্ডকরণ : মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে একটি কাঠের সঙ্গে বেঁধে ঘোড়া দিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জায়গায়, অর্থাৎ বধ্যভূমিতে। এরপরে সেই ব্যক্তিকে ঝুলিয়ে দেওয়া হত ফাঁসির দড়িতে। মৃত্যু হওয়ার আগেই সেই ব্যক্তির গলা থেকে ফাঁসির দড়ি থেকে খুলে দেওয়া হত। এ অবস্থায় তাঁকে জলে ডুবানো হত। এরপরও মৃত্যু না হলে আধমরা ব্যক্তিকে হাত-পা বেঁধে তাঁর পেট কেটে পেটের মধ্য থেকে ভুড়ি বের করে আনা হত। এসময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখা হত যেন কোনোভাবেই তাঁর মূল রক্ত পরিবাহীতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। ফলে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যু হত না। এরপর মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অর্ধমৃত ব্যক্তির নাড়িভূঁড়িতে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হত। এরপর ধারালো কুড়োল দিয়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জীবন্ত অবস্থায় কেটে চার টুকরো করা হত। সবশেষে তাঁর মাথা কেটে ফেলা হত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মাথা কাটার আগে পর্যন্ত মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিটি বেঁচে থাকত। এখানেই শেষ নয়, এরপরে তাঁর দেহের বিভিন্ন অংশ ইংল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠিয়ে দেওয়া হত, জনগণকে দেখানোর উদ্দেশ্যে। বীভৎস এই নরহত্যা হত রাষ্ট্রের নির্দেশে, শাসনের নামে। ফাঁসি, জলে ডুবানো, খণ্ডকরণ পদ্ধতিতে একসঙ্গে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা ইতিহাসে সব থেকে অমানবিক পন্থা বলে বিবেচিত। বর্তমানে এই পদ্ধতিটি আর কার্যকর হয় না।
এখন মৃত্যুদণ্ড পদ্ধতি নিয়ে নীচে যে আলোচনা করব যেগুলি বর্তমানে প্রচলিত না থাকলেও প্রাচীন যুগে ছিল।
(৬) মুণ্ডচ্ছেদ বা শিকর্তন : মুণ্ডচ্ছেদ বা শিল্পকর্তন (Guillotine) পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পদ্ধতি মূলত চালু করা হয় মানবিক দিক বিবেচনা করে। ১৭০০ শতকে এই পদ্ধতি চালু করা হয়, কেননা তৎকালীন আমলে বিশেষজ্ঞদের মতে এই পদ্ধতিতে আসামীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হলে তাঁর কষ্ট কম হয়! তাই তৎকালীন সময়ে অনেক দেশ এই পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে থাকে। কোনো মানুষ দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁর মুণ্ডচ্ছেদ করাই ছিল এই গিলোটিনের কাজ। ডা. জোশেফ ইগনেস গিলোটিন ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম এই মারণযন্ত্রের প্রবর্তন করেন। ফরাসি বিপ্লব চলাকালীন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত দোষীকে শাস্তি দেওয়ার জন্য তিনি এই অভিনব যন্ত্রটির সুপারিশ করেন। আজ থেকে প্রায় ২৩০ বছর আগে অর্থাৎ ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ১৪ জুলাই বাস্তিল দুর্গে বন্দুকের আওয়াজের মধ্যে ফরাসি বিপ্লবের নতুন অধ্যায়ের সূচনা। তার ২ বছর পর ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে সে দেশের রাজা ষোড়শ লুই ছদ্মবেশে ভার্নেতে পালাতে গিয়ে ধরা পড়েন জুন মাসের ২০ তারিখে। তার ঠিক এক বছর সাত মাসের মাথায় ২১ জানুয়ারি রাজাকে ধরে গিলোটিনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে রাজার মুণ্ড। এভাবে কত যে মানুষের মুণ্ডচ্ছেদ হয়েছে তার শেষ নেই। এজন্যই ফরাসি বিপ্লবের কাহিনি থেকে গিলোটিনকে কিছুতেই আলাদা করা যায় না। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে ২৫ এপ্রিল ডি গ্রিভ শহরের উন্মুক্ত প্রান্তরে এটিকে স্থাপন করা হয় এবং সর্বপ্রথম একজন হাইওয়ে ম্যান’-এর মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়। এরপর ওই বছরই পেরিসের ডি লা কনকর্ডে প্রায় ৪০০০ মানুষের শিরচ্ছেদ হয় একইভাবে। উল্লেখযোগ্যতার মধ্যে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারিতে রাজা ষোড়শ লুইয়ের পর ১৬ অক্টোবর রানি মারি আঁতোয়ানে, ৩১ অক্টোবর জিরাদের, ৮ নভেম্বর মাদাম রোঁলা, ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দে ৩০ মার্চ থেকে ৫ এপ্রিলের মধ্যে জর্জ দাঁত ও তাঁর অনুগামীদের গিলোটিনে হত্যা করা হয়। চাকা কীভাবে ঘোরে! দাঁতে ও তাঁর পন্থীদের গিলোটিনে পাঠানোর মূল হোতা যে বিপ্লবী নায়ক ব্যারিস্টার মেক্সিমলিয়ন মারি ইশিদর দ্য রোবসপিয়েরকেও সেই নিমর্ম গিলোটিনে মাথা দিতে হয়। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা বন্ধ হয়ে যায়। ফ্রান্সে গিলোটিনে শেষ মৃত্যুটি হয় ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে। ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই গিলোটিনে মৃত্যুর হার কমে আসে। ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সে মৃত্যুদণ্ড নিষিদ্ধ হয় ও সেইসঙ্গে মুণ্ডচ্ছেদও বন্ধ হয়ে যায়। ডা. গিলোটিনও খুব অল্পের জন্য গিলোটিন যন্ত্রে মৃত্যু থেকে বেঁচে যান।
(৭) হাতির পায়ে পিষ্ট করে মৃত্যুদণ্ড : মৃত্যদণ্ড কার্যকর করার এই পদ্ধতি কিন্তু সুদুর কোনো দেশের প্রচলিত পদ্ধতি না, বরং আমাদের এই দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় উদ্ভাবিত এবং একসময়ের বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে বিশাল আকৃতির হাতি তার পা দিয়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির মাথা থেঁতলে দিত। এক্ষেত্রে হাতিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হত, যাতে সে ধীরে ধীরে পায়ের চাপ বাড়ায়, যাতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি সর্বোচ্চ শাস্তি পায় মৃত্যুর সময়। এই পদ্ধতি মূলত ব্যবহৃত হত রাজা বাদশাহদের আমলে।
(৮) শরীরের চামড়া ছাড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড : মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির চামড়া ছাড়ানো (Flaying Skin) ছিল এক বীভৎস মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জীবিত অবস্থায় একটা লম্বা টেবিলের উপর বেঁধে তাঁর চামড়া ছাড়ানো হয়। এই ছাড়ানো চামড়া জনবহুল এলাকায় প্রকাশ্যে টানিয়ে রাখা হত, যাতে সবাই দেখতে পারে এবং শাসককে ভয় পায়।
(৯) স্কাফিজম : অতীতে পার্সিয়ানদের মধ্যে প্রচলিত মৃত্যদণ্ড কার্যকর করার পদ্ধতিই হল স্কাফিজম (Scaphism)। এ পদ্ধতির মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে একটি ডোবার কাছে আনা হত। এরপর ডোবার সব থেকে কাছের গাছের সঙ্গে বেঁধে রাখা হত। এরপর সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রচুর পরিমাণে দুধ এবং মধু খাওয়ানো হত, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর ডাইরিয়া শুরু হত। ডাইরিয়া শুরু হলে তাঁর সারা শরীরে মধু মাখিয়ে দেওয়া হত। এই মধু মেখে দেওয়ার ফলে আশেপাশের অনেক বিষাক্ত কীটপতঙ্গরা আকৃষ্ট হত এবং মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির গায়ের চামড়া ভেদ করে বাসা বানাত। এই পদ্ধতিতে আসামীর মৃত্যু হতে সময় লাগত ২ সপ্তাহের মতো। সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তিটির ডাইরিয়া, গ্যাংগ্রিন এবং অনাহারে মৃত্যু হত।
(১০) তক্তার উপর : এই উপায়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করত সাধারণত জলদস্যুরা, যাঁরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাহাজ আক্রমণ করে জাহাজের সব কিছু লুট করে নিত। আর যাঁরা তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলত তাঁদের এইভাবে শাস্তি দেওয়া হত। এক্ষেত্রে ব্যক্তিকে শুধুমাত্র তক্তার উপর দিয়ে হাঁটিয়ে জলে ফেলে দেওয়া হত। কিন্তু তাঁর হাত-পা কিছুই বাঁধা থাকত না বলে জলে ভেসে থাকতে পারত। কিন্তু জলে ভাসমান এইসব জাহাজের চারিপাশে সবসময় কিছু হাঙ্গর ঘুরে বেড়াত, আর জলে ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই হাঙ্গরের বলি হত এবং মৃত্যু কার্যকর হত।
(১১) মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে করাতের ব্যবহার : এই পদ্ধতি আগে চালু ছিল ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশগুলিতে। এক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ নগ্ন করে উল্টো করে দুই পা দুই দিকে ফাঁক করে বেঁধে রাখা হত। এরপর মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির যৌনাঙ্গ বরাবর করাত রেখে দেহকে মাঝ বরাবর কেটে ফেলা হত। আর উল্টো করে ঝোলানোর কারণে ব্যক্তিটির মস্তিষ্ক যথেষ্ট পরিমাণ রক্ত পেত, যাতে ব্যক্তিটি এই শরীরের মাঝ বরাবর কেটে ফেলায় ব্যথা সম্পূর্ণটাই অনুভব করতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কাটার আগে পর্যন্ত তিনি বেঁচে থাকতেন।
(১২) রিপাবলিকান ম্যারেজ : রিপাবলিকান বিবাহ (Republican Marriage) হল মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার এক অভিনব পদ্ধতি। এই পদ্ধতি হল একজন পুরুষ এবং মহিলাকে নগ্ন করে এবং মুখোমুখি করে একসঙ্গে বেঁধে নদীর জলে ফেলে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা। শুধুমাত্র ফ্রান্সে এই পদ্ধতি চালু ছিল।
(১৩) বেস্টিয়ারাই মৃত্যুদণ্ড : বেস্টিয়ারাই (Bestiari), আদি রোমান সাম্রাজ্যের একটা ক্রীড়া। যেখানে বীরেরা হিংস্র প্রাণীর মুখোমুখি হয়ে তাদের পরাস্ত করত। কিন্তু এই ক্রীড়াকেও ব্যাবহার করা হত মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের উপায় হিসাবে। যে সমস্ত ব্যক্তিদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত তাঁদের সম্পূর্ণ নগ্ন করে ছেড়ে দেওয়া হত হিংস্র প্রাণীদের মধ্যে এবং কোনোরূপ প্রতিরোধ ছাড়াই হিংস্র প্রাণীরা মেরে ফেলত মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে এবং অবশ্যই খেয়ে ফেলত। এই মৃত্যু দেখে এই ক্রীড়া দেখতে আসা দর্শকেরা উল্লাসে গলা ফাটাত। মৃত্যুও বিনোদন, ভাবা যায়!
(১৪) নিষ্পেষণে মৃত্যুদণ্ড : নিষ্পেষণ (Crushing) পদ্ধতি মূলত মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার হত না, তবে যে সকল ব্যক্তির উপর ব্যবহার করা হত তাঁরা সকলেই মৃত্যুবরণ করত। এই পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল আমেরিকায়। আর সেখান থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এটির প্রসার ঘটে। তৎকালীন সময়ে কোনো সাধারণ ব্যক্তি যদি কোনো সম্ভ্রান্ত পরিবারের বিশেষ ব্যক্তিদের দ্বারা দোষী হিসাবে আখ্যা পেত, তাহলে তাঁদের দিয়ে দোষ স্বীকার করানোর কাজেই ব্যাবহার করা হত এই পদ্ধতি। এক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিটিকে মাটিতে শুইয়ে তাঁর শরীরের উপর ভারী বস্তু রাখা হত এবং প্রতিবার তাঁকে তাঁর দোষ স্বীকার করার কথা বলা হত। স্বীকার না করা পর্যন্ত ওজন বাড়িয়ে যাওয়া হত, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে মারা যায়। তবে দোষ স্বীকার করলেও যে মুক্তি পেত তা নয়, সেই দোষের জন্য এবং সবাইকে মিথ্যা বলার দায়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হত।
(১৫) সিমেন্টের জুতো পরিয়ে মৃত্যুদণ্ড : এই জুতো যেই-সেই জুতো নয়, সিমেন্টের তৈরি। এই পদ্ধতি অনেকটাই রিপাবলিকান ম্যারেজ’ পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার মতো, অর্থাৎ নদীর জলে ডুবিয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা। শুধু পার্থক্য হল এখানে বিপরীত লিঙ্গের কারও সঙ্গে না বেঁধে, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির পায়ে পরিয়ে দেওয়া হবে সিমেন্টের জুতো, যাতে ব্যক্তিটি জলের মধ্যে ভেসে থাকতে না পারেন। এই পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সবচেয়ে বেশি প্রচলন ছিল আমেরিকার মাফিয়াদের মধ্যে।
(১৬) ব্লাড ঈগল : ফিনল্যান্ডে রক্তের ঈগল বা Blood Eagle পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার প্রথা চালু ছিল। এই পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দাঁড় করিয়ে টান টান করে বেঁধে তাঁর মেরুদণ্ড বরাবর কেটে তাঁরই বুকের পাঁজর ভেঙে ঈগলের পাখার মতো মেলে রাখা হত। এরপরে পিছন থেকে ফুসফুস বের করে রাখা হত। এখানেই শেষ না, এরপরে বাইরে ঝুলে থাকা ফুসফুস এবং ক্ষত জায়গায় লবণ মাখিয়ে দেওয়া হত। এই পদ্ধতিতে রক্তক্ষরণ কম হওয়ার কারণে ব্যক্তি অনেক সময় ধরে বেঁচে থাকত এবং মৃত্যুর তীব্রতাও বৃদ্ধি পেত।
(১৭) ন্যায়ের ঝাঁকি : ন্যায়ের ঝাঁকি বা Upright Jerker পদ্ধতি প্রথম চালু হয় আমেরিকাতে। কিন্তু আমেরিকাতে বর্তমানে এই পদ্ধতি নিষিদ্ধ হলেও বর্তমানে ইরানে এই পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রকাশ্যে গলায় দড়ি পরিয়ে দড়িটি উপরে দিকে টেনে তোলা হয়। দড়িটি তোলার সময় ঝাঁকি দেওয়া হয়, যাতে আসামির ঘাড় ছিঁড়ে যায়। দড়িটি তুলতে সাধারণত ক্রেন ব্যবহার করা হত।
(১৮) মাজাটেল্লো : অত্যন্ত বীভৎস এই পদ্ধতি। মাজাটেল্লো বা Mazzatello হল এমনই একটি মৃত্যুদণ্ড প্রক্রিয়া। এ পদ্ধতি হল শহরের মাঝে উঁচু মঞ্চে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে আনা হত এবং তাঁর মাথায় কাঠের তৈরি এক হাতুড়ি দিয়ে জোরে আঘাত করা হত। তারপর আঘাতে আঘাতে মাথা থেঁতো করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হত। অষ্টাদশ দশকের দিকে ইউরোপের যে সমস্ত দেশে যেখানে পোপের আইন চালু ছিল, সেখানেই এই প্রক্রিয়া চালু ছিল।
(১৯) জাফরি : জাফরি বা Gridiron পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জ্বলন্ত কয়লার বিছানার উপর জোড় করে চেপে রাখা হত। যতক্ষণ-না মৃত্যু হত ততক্ষণ পর্যন্ত এইভাবে জ্বলন্ত কয়লার বিছানায় শুইয়ে রাখা হত। এই পদ্ধতি বহুক্ষণ ধরে চলত। মৃত্যুও আসত অনেক দেরিতে। তারপর শরীরের চামড়া পুড়ে সম্পূর্ণটাই কালো হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি।
(২০) ক্যাথেরিনের চাকা : ক্যাথেরিনের চাকা বা Catherin wheel বা Breaking wheel পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হল মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ শাস্তি প্রদান করা। এই পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে একটি চাকার সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা দেওয়া হত। এরপর চাকাটি খুব জোরে ঘুরিয়ে দেওয়া হত। এ সময় জল্লাদ ঘুরতে থাকা মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে শরীরে চাবুক বা লাঠি দিয়ে সজোরে উপযুপরি আঘাত করা হত। এরপর জল্লাদ মোটা লোহা দিয়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে হাতে আর পায়ে পেরেক পুঁতে দিত। পুনরায় চাবুক আর লাঠি দিয়ে আঘাত করত জল্লাদ। এরপর পেরেক পোঁতা অবস্থায় ব্যক্তিকে শহরের মাঝে জনসমক্ষে ঝুলিয়ে রাখা হত, যাতে সকলে এই নির্মমতা দেখতে পারে।
(২১) বাঁশ : এশিয়ার দেশগুলিতে একসময় মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার ক্ষেত্রে বাঁশের ব্যবহার হত। মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার এক অভিনব এবং খুবই কষ্টদায়ক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে বাঁশের সঙ্গে শক্ত করে বেঁধে রাখা হত। যেহেতু বাঁশ গাছ অনেক তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় (দৈনিক সর্বোচ্চ এক ফুটের মতো), তাই ধীরে ধীরে ছোটো বাঁশ ব্যক্তির দেহ ফুটো করে বের হয়ে যেত। এটি বেশ ধীরে হত বলে ব্যক্তিটি অমানবিক যন্ত্রণা পেত এবং মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হত।
(২২) সুড়সুড়ি : স্প্যানিসদের সুড়সুড়ি যন্ত্র বা Spanish Tickler বা বিড়ালের থাবা বা Cat’s Paw পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ড পদ্ধতির উৎপত্তি স্প্যানিসে। এঁদের দ্বারাই ব্যবহৃত হওয়ার কারণে ‘স্প্যানিসদের সুড়সুড়ি যন্ত্র’ নামেই বেশি পরিচিত। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে শক্ত করে বেঁধে রাখা হত শহরের জনবহুল এলাকায়। তারপর জল্লাদ এই সুড়সুড়ি দেওয়ার যন্ত্র’ পরে যথেচ্ছভাবে ব্যক্তিটির শরীরে আঁচড় দিত। এই আঁচড় যে সে আঁচড় নয়, এক্কেবারে শরীর থেকে চামড়া আলাদা হয়ে যেত। কিন্তু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হত না এত সহজে। দীর্ঘক্ষণ মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করতে হত। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যু হত মূলত রক্তক্ষরণের কারণে। ইনফেকশনের কারণেও মৃত্যু হত।
(২৩) জীবিত কবর : প্রেমের অপরাধে আনারকলিকে জীবিত অবস্থায় কবর দেওয়া হচ্ছে, মুঘল-ই-আজম’-এর এ দৃশ্যটি নিশ্চয় কেউ ভুলে যাননি। এমনই জীবিত কবর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পদ্ধতিটি মধ্যযুগের ইতিহাসে অনেক রাষ্ট্র গ্রহণ করেছিলেন। এহেন জীবিত অবস্থার কবর ঠিক আনারকলির মতো নয়। সাধারণত বিদ্রোহীদের বা একাধিক হত্যাকারী বা ধর্ষণকারীদের এইভাবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হত। সর্বশেষ এরকম কবর দেয় জাপানিরা, যখন তাঁরা চিনে হামলা করেছিল তখন অনেক চাইনিজদের উপর এইভাবে মৃত্যদণ্ড পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।
(২৪) বেঁধে পোড়ানো : খুঁটির সঙ্গে বেঁধে পোড়ানো বা Burning at the Steak পদ্ধতিটি মৃত্যুদণ্ড হিসাবে জনপ্রিয়(!) ছিল। মৃত্যদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের একা অথবা একই সঙ্গে অনেককে পুড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হত। ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে জিওনার্দো ব্রুনো (১৫৪৮-১৬০০) নামে এক জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে রোমে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদকে সমর্থন করার অপরাধে’ জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। ব্রুনোকে আগুনে পোড়ানোর আগে পর্যন্ত চার্চ থেকে প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছিল যেন তিনি কোপার্নিকাসের ভুল মতবাদ পরিত্যাগ করে বাইবেলের বিশ্বাসের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ টলেমির ‘পৃথিবী কেন্দ্রিক মতবাদকে সত্য বলে মেনে নেন। বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতি অবিচল ব্রুনো ঘৃণাভরে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বরং বিচারকদের দিকে তাকিয়ে অবিচলভাবে ব্রুনো উচ্চারণ করেছিলেন –“Perhaps you, my judges, pronounce this sentence against me with greater fear than I recieve it.” বোঝাই যাচ্ছে, ব্রুনোর নশ্বর দেহ যখন আগুনের লালচে উত্তাপে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল, “ধর্ম বেঁচে গেল” ভেবে ধর্ম-ব্যবসায়ীরা কী উল্লাসই-না প্রকাশ করেছিল সেদিন। তারপরেও ঈশ্বর এবং তাঁর সন্তানেরা সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর ঘূর্ণন শেষপর্যন্ত কি থামাতে পেরেছিলেন?
(২৫) নির্লজ্জ ষাঁড় : নির্লজ্জ ষাঁড় বা Brazen Bull পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা আর-একটি অমানবিক পদ্ধতি। সিসিলির স্বৈরশাসক Akgragas এই পদ্ধতি প্রথম চালু করেছিলেন। পরামর্শদাতা ছিলেন তৎকালীন সময়ের ধাতু কারুকার্যকর প্রিলিয়স (Prilios)। ধাতু দ্বারা নির্মিত এই ষাঁড়কে এতটা বড়ো করে বানানো হত যেন এর পেটের মধ্যে একজন মানুষকে ঢোকানো সম্ভব হয়। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ওই ষাঁড়ের পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে পেটের দিকে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হত। এর ফলে ষাঁড়ের ভিতরে থাকা মানুষটি ধীরে ধীরে সরাসরি আগুনে না ঝলসে আগুনের গনগনে তাপে মারা যেত। ষাঁড়টিকে এমনভাবে নির্মাণ করা হত যাতে ভিতরে পুড়তে থাকা ব্যক্তিটির চিৎকার শুনে মনে হত যেন ষাঁড় চিৎকার করছে। পুড়তে থাকা ব্যক্তিটির ধোঁয়া ষাঁড়ের নাক দিয়ে বেরিয়ে আসত।
(২৬) লিং চি : লিং চি বা Ling Chi মৃত্যুদণ্ড পদ্ধতিটি চিনে চালু ছিল। এই পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে লোকালয়ে এনে বেঁধে ফেলত। এরপর একজন জল্লাদ বিশেষ ছুরি দিয়ে ব্যক্তির বিভিন্ন অঙ্গ তার দেহ থেকে ধীরে ধীরে আলাদা করে দিত। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি যাতে দীর্ঘক্ষণ ধরে সর্বাধিক যন্ত্রণা ভোগ করে সে ব্যাপারে নিশ্চিত করা ছিল জল্লাদের প্রধান উদ্দেশ্য। এ পদ্ধতি এখন আর কার্যকর করা হয় না। চিনেই ২০ সহস্রাব্দের শুরুতে এই পদ্ধতি নিষিদ্ধ হয়ে গেছে।
(২৭) কলম্বিয়ার নেকটাই : এই পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় শুধুমাত্র মাদক ব্যবসায়ীদের জন্য। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির গলা কাটা হয়, সেই কাটা অংশ থেকে ব্যক্তির জিভ বের করে রাখা হত। প্রকাশ্যে প্রদর্শনীর জন্যেও রাখা হত। যাতে অন্যান্য মাদক ব্যবসায়ীদের মধ্যে ভয়ের সৃষ্টি হয়। কলম্বিয়ার নেকটাই বা Colombian Necktie পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পদ্ধতি এখনও কলম্বিয়া সহ লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে প্রচলিত আছে।
(২৮) সেপপুকু : সেপপুকু বা Seppuku মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার পদ্ধতি আসলে আত্মহত্যার সামিল। জাপানের সামুরাইদের মধ্যে বেশি প্রচলিত। এই পদ্ধতিতে মৃত্যুবরণ করা অনেকটা সম্মানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করার পর্যায়ে পরে। সামুরাই নিজের তলোয়ার দিয়ে নিজের পেটে আঘাত করে নিজের পেটের ভিতর দিয়ে নাড়িভুঁড়ি বাইরে বের করে নিয়ে আসে। সে সময় তাঁর কাছের কোনো বন্ধু তলোয়ার দিয়ে এক কোপে আত্মহত্যাকারীর মাথা শরীর থেকে পৃথকটা করে ফেলত। এহেন মৃত্যুবরণ করা অমানবিক মনে হলেও মৃত্যুবরণকারী সামুরাইয়ের কাছে এটি অনেক সম্মানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করা এবং তাঁর বন্ধুর কাছে বন্ধুর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানানো।
(২৯) ক্রুশকাঠে বিদ্ধ করা : ক্রুশকাঠে বিদ্ধ করে হত্যা বা Crucifixion যদিও ধর্মীয়ভাবে খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের কাছে অনেক পবিত্র। মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত সমস্ত ব্যক্তিকে এভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। এটি ছিল রোমানদের সব থেকে জনপ্রিয় পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার আগে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অনেক অত্যাচার করা হয়। তারপর তাঁকে বাধ্য করা হত তাঁকে যে ক্রুশকাঠে ঝোলানো হবে সেই ক্রুশকাঠটিকে নিজের কাঁধে করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। এরপর তাঁকে ক্রুশকাঠের উপর শুইয়ে তাঁর দু-হাতের তালু বরাবর লোহার পেরেক পুঁতে দেওয়া হত। এছাড়াও তাঁর দু-পা এক জায়গায় এনে লোহার পেরেক পুঁতে দেওয়া হত খুঁটির সঙ্গে। এভাবেই মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঝুলে থাকত মৃত্যু না-হওয়া পর্যন্ত। সাধারণত সপ্তাখানেক সময় লাগত মৃত্যু হতে। মৃত্যু সম্পন্ন হত শ্বাস বন্ধ হয়ে। জিশুখ্রিস্ট এভাবেই ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা যান। এই ধারণা থেকেই খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের কাছে ক্রুশ একটি পবিত্র চিহ্ন বা প্রতীক। কিন্তু খ্রিস্টজন্মের বহু আগে থেকেই রোমান সভ্যতায় খুঁজে পাওয়া যায় ইংরেজি ‘T’ অক্ষর সদৃশ তিনবাহু বিশিষ্ট মানুষ হত্যা করার বিশেষ অস্ত্র বিশেষ। উল্লেখ্য, ‘T’ থেকেই ক্রুশচিহ্ন এর সৃষ্টি হয়েছে এমন দাবি কারও পক্ষেই জোর করে করা সম্ভব নয়। তবে দুটি প্রতাঁকের কাজের মিল এবং গাঠনিক মিল বেশ স্পষ্টভাবেই দৃশ্যমান। অনেকেই মনে করে থাকেন। জিশুখ্রিস্টর ক্রুসিফিকেশন ইতিহাসের প্রথম নির্মম হত্যাকাণ্ড। কিন্তু তাঁদের এই ধারণা সম্পূর্ণই ভুল। আসিয়রিয়ান, গ্রিক এবং পারসিয়ান সভ্যতায় ভুরি ভুরি উদাহারণ খুঁজে পাওয়া যায় কুসিফিকেশন করে দেশদ্রোহী এবং ক্রীতদাসদের হত্যা করার জন্য।
(৩০) বিষাক্ত ইনজেকশন : মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রথমে স্নান করিয়ে তাঁকে শেষ খাবার দেওয়া হয় এবং তাঁর নিজ ধর্ম অনুযায়ী প্রার্থনা করানো হয়। পরে তাঁকে একটা ছোটো চেম্বারে নিয়ে একটা বিছানার সঙ্গে বাঁধা হয়। তাঁর শরীরে দুটো নল ঢুকানো হয় ইনজেকশনের মাধ্যমে। তাঁর শরীরে প্রথমে সোডিয়াম থিওপেনটাল ৫০০০ মিলিগ্রাম দেওয়া হত, যা এনেসথেসিয়ার কাজ করে। তারপরে পানকুরিয়াম ব্রোমাইড দেওয়া হত ফুসফুস অবশ করার জন্য। এর পরে দেওয়া হত পটাশিয়াম ক্লোরাইড, হৃৎপিণ্ড বন্ধ হওয়ার জন্য।
(৩১) পাথর নিক্ষেপ : এ পদ্ধতিতে পুরুষের ক্ষেত্রে কোমর পর্যন্ত এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে বুক পর্যন্ত মাটিতে পোঁতা হয়। কাছ থেকে মাঝারি সাইজের পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হত। পাথর যেন খুব বড়ো না হয়, যাতে হঠাৎ করেই ওই ব্যক্তি মারা না যায়। তবে নিয়ম আছে যে, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি যদি পাথর নিক্ষেপের সময় গর্ত থেকে উঠে আসতে পারে, তবে তাঁর মৃত্যুদণ্ড মকুব হয়ে যাবে।
(৩২) বিষপান : বিষ পান করিয়েও অনেক দেশে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হত। এ বিষয়ে আমরা দার্শনিক সক্রেটিসের কথা মনে করতে পারি। গ্রিসের এথেন্সে তখনকার দিনের অন্যতম রাজনীতিবিদ আনুতুস তাঁর বিরুদ্ধে মুখ্য অভিযোগ আনেন যে, তিনি রাষ্ট্রের তরুণ সম্প্রদায়ের মনে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র এবং সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে সন্দেহ, অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার ভাব সৃষ্টি করে চলেছেন। এসব অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে তিনি বিচারকদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। বিচারকদের বিচারে দোষী প্রমাণিত হলে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হতে পারে। এথেন্সের কেন্দ্রবিন্দুতে বসেছে এই আদালত। আদালতের বিচারকের সংখ্যা ৫০০। বিচারকরা আসীন কাঠের বেঞ্চিতে। বিচারকদের চারপাশ ঘিরে উৎসুক জনতার ভিড়। সক্রেটিসের বিরুদ্ধে অভিযোগকারী তিন এথেনীয় নাগরিকও সেখানে হাজির। তিন অভিযোগকারীকে তাঁদের অভিযোগ উত্থাপন করে বক্তব্য রাখার জন্য তিন ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়। এরপর সক্রেটিসকে সময় দেওয়া হবে তিন ঘণ্টা, তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ খণ্ডনের জন্য। বিচারকরা অভিযোগের সত্য-মিথ্যা নির্ধারণে ভোটের মাধ্যমে তাঁদের রায় জানাবেন। বিচারকদের সামনে দুটি গোলাকার কলসি। একটিতে লেখা ‘guilty’, আর অপরটিতে ‘not guilty’। বিচারকরা তাঁদের ইচ্ছেমতো যে-কোনো একটি কলসিতে তাঁদের নিজ নিজ চাকতি ফেলে সক্রেটিসের বিচারের রায় সমাধা করবেন। এভাবে ভোটভিত্তিক আদালতের রায়ে সক্রেটিসের পক্ষে ২২০ বিচারক ও বিপক্ষে ২৮০ বিচারকের ভোট পড়ে। অতএব বিচারে সক্রেটিস দোষী সাব্যস্ত হন। এরপর এল সক্রেটিসের শাস্তি নির্ধারণের পালা। অভিযোগকারীরা সক্রেটিসের মৃত্যুদণ্ড দাবি করে। সক্রেটিসকে সুযোগ দেওয়া হয়, তাঁর বিরুদ্ধে কী ধরনের শাস্তি হতে পারে, সে ব্যাপারে পরামর্শ রাখার জন্য। অনেকে ধরে নিয়েছিলেন সক্রেটিস হয়তো বলবেন তাঁকে মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে নির্বাসনে দেওয়া হোক। তা না-করে সক্রেটিস বরং সেদিন বলেছিলেন, তিনি ভণ্ড জ্ঞানীদের মুখোশ খুলে দিচ্ছেন। সক্রেটিসের নিজের ভাষায় : “রাষ্ট্ররূপ মন্থরগতি অশ্বের জন্য আমি হচ্ছি বিধিদত্ত এক ডাঁশ পোকা।” অতএব তাঁকে পুরস্কৃত করাই উচিত। এমনি পরিস্থিতিতে তাঁর উপর চাপ আসে বাস্তবভিত্তিক কোনো শাস্তির পরামর্শ দিতে। তখন তিনি চাপের মুখে বলেন, তাঁকে মোটা দাগে জরিমানা করা যেতে পারে। বিচারকরা শেষপর্যন্ত তাঁর মৃত্যুদণ্ডই ঘোষণা করেন। নিজ হাতে বিষ পান করে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। রায় ঘোষণার পর তাঁকে কাছাকাছি একটি কারাগারে নেওয়া হয়। এথেনীয় আইন অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুদণ্ড সেখানেই কার্যকর করা হয়। আর সক্রেটিস নিজ হাতে হেমলক বিষপান করে তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন। মৃত্যুর আগে তিনি বিষপাত্র হাতে নিয়ে বলেছিলেন : “I to die, you to live, but only God knows who is correct.”
(৩৩) শূলে চড়ানো : শূলে চড়ানো’ বা ‘শূলবিদ্ধ করা একটি প্রাচীন শাস্তি বা মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পদ্ধতি। নিঃসন্দেহে এটি ছিল ভয়াবহ ও বর্বরোচিত শাস্তি। প্রথম শূলে চড়ানোর ইতিহাস পাওয়া যায় প্রাচীন নিকট প্রাচ্যে। সে সময় রাজদ্রোহীদের শূলে চড়িয়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। তৎকালীন পারস্যের রাজা প্রথম দারায়ুস ব্যাবিলন জয় করার পর প্রায় ৩ হাজার ব্যাবিলনবাসীকে শূলে চড়িয়েছিলেন। একটি সুচালো দণ্ড বা খুঁটিকে দেহের ছিদ্রপথে বিশেষ করে পায়ুপথে প্রবেশ করানো হত। তারপর খুঁটিটিকে মাটিতে গেঁড়ে দেওয়া হত। একসময় সুচালো অংশটি অপরাধীর শরীর ভেদ করে বুক অথবা ঘাড় দিয়ে বের হয়ে যেত। অপরাধী ব্যক্তিটি এভাবে একসময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত। অনেক সময় খুঁটিটির মাথা সুচালো না-করে ভোঁতা রাখা হত, যাতে হৃৎপিণ্ড বা অন্যান্য প্রধান অঙ্গ বিদ্ধ হয়ে তাড়াতাড়ি মারা না যায়। এতে অপরাধী বেশি কষ্ট পেত। কেননা মারা যেতে কয়েক ঘণ্টা এমনকি একদিন সময়ও লাগত। শূলে চড়ানোর মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি কুখ্যাত ছিল প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের ওয়ালেশিয়া রাজ্যের যুবরাজ তৃতীয় স্লাদ, যাকে বলা হত ড্রাকুলা। তৎকালীন তুরস্কেও এ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। তুর্কিদের হাতে একবার আটক হওয়ার সময় তৃতীয় স্লাদ মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার এ পদ্ধতিটি শিখে নেয়। ড্রাকুলা যুদ্ধবন্দি ও রাজদ্রোহীদের শূলে চড়াত সাধারণ প্রজাদের সামনেই, যাতে তাঁরা ড্রাকুলাকে ভয় পায়। তাঁর শত্রুদের জন্যও এটা ছিল তাঁর প্রতি ভয়াবহতার ইঙ্গিত। তবে ড্রাকুলার শূলে চড়ানোর পদ্ধতি ছিল ভিন্নতর। পেট অথবা পিঠের মধ্য দিয়ে সুচালো কোনো দণ্ড ঢুকিয়ে দিয়ে তা মাটিতে গেঁড়ে দেওয়া হত। এভাবে একসঙ্গে অনেক মানুষকে শূলে চড়িয়েছেন ড্রাকুলা। আফ্রিকান উপজাতি জুলুদের মধ্যে শূলে চড়ানো প্রচলিত ছিল। জাপান, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়ায়ও একসময় এ পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। পাক-ভারত উপমহাদেশের ভারতের তামিলনাড় ও কেরল প্রদেশে নিকট অতীতে শূলে চড়ানোর মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত।
(৩৪) চূর্ণ বা পিষ্টকরণ : চূর্ণকরণ বা Crushing কোনো কিছু চাপা দিয়ে পিষ্ট করার ব্যাপারটা ইউরোপ, আমেরিকায় বেশি প্রচলন ছিল। সাধারণত জোরপূর্বক কিছু আদায় করার ক্ষেত্রে তাঁরা এই শাস্তিটি ব্যবহার করত। এই পদ্ধতিতে বন্দিকে মাটির সঙ্গে শুইয়ে তাঁর শরীরের উপর কাঠের তক্তা রাখা হত এবং কাঠের তক্তার উপর ভারী ভারী পাথর রাখা হত। ততক্ষণ পর্যন্ত এই শাস্তি চলতে থাকত যতক্ষণ-না বন্দি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত।
(৩৫) বিশাল পাথর বেঁধে জলে নিক্ষেপ করে মৃত্যুদণ্ড : প্রাচীনকালে অপরাধ করলে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সমুদ্র বা নদীর জলে ডুবিয়ে মারা হত। যাতে জলের উপর ভেসে উঠতে না পারে এবং সাঁতরে পালিয়ে যেতে না পারে সেই কারণে ব্যক্তির শরীরের সঙ্গে বিশাল পাথরের চাঁই দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হত। সেই পাথরের ভারে ব্যক্তির দেহ জলের অতলে তলিয়ে যেত। ভাগবতপুরাণে বর্ণিত হিরণ্যকশিপু-কায়াদু পুত্র প্রহ্লাদকে বিষ্ণুভক্ত হওয়ার অপরাধে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নেয় পিতা হিরণ্যকশিপু স্বয়ং। কিন্তু যতবারই তিনি বালক প্রহ্লাদকে বধ করতে যান, ততবারই বিষ্ণুর মায়াবলে প্রহ্লাদের প্রাণ রক্ষা পায়। তারই মধ্যে প্রহ্লাদকে শরীরে পাথর বেঁধে জলে নিক্ষেপ করা ছিল একটি উপায়। যদিও সব উপায়ই ব্যর্থ হয়েছিল গল্পের খাতিরে। বাস্তবে কিন্তু। বাঁচার কোনো উপায় নেই।
(৩৬) ঘোড়ার পিছনে বেঁধে : মধ্যযুগে রাজা সম্রাটরা মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর দুই পায়ে শক্ত দড়ি বেঁধে দুটি ঘোড়ার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হত। এরপর ঘোড়া দুটিকে ছুটিয়ে দেওয়া হত। দুটি ঘোড়া দু-দিকে তীব্র বেগে ছুটে যাওয়ার সময় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির পা ছিঁড়ে শরীর দু-ভাগ হয়ে মারা যেত।
লোমহর্ষক বটে! যেসব গ্রন্থগুলিকে আমরা ধর্মশাস্ত্র বা কিতাব বলি, সেগুলি আসলে আইন– অনুশাসন গ্রন্থ। বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় যেটাকে আমরা আইনগ্রন্থ বা সংবিধান বলি। বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার অনুশাসনগুলি ঈশ্বর বা আল্লার নামে প্রয়োগ করা হলেও, বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় অনুশাসন চলে রাষ্ট্রের নামে। তথাকথিত ধর্মানুশাসন যেমন বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুসারে পরিবর্তন/সংযোজন/বর্জন করা হত, ঠিক তেমনি বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থাতেও অনুশাসন বা আইনের ধারাগুলি পরিবর্তন/সংযোজন/বর্জন করা হয় প্রয়োজন অনুসারে। পার্থক্য হল ধর্মীয় অনুশাসনগুলি যতটা শ্রদ্ধার সঙ্গে মান্য করে চলে মানুষ, রাষ্ট্রব্যবস্থায় অনুশাসন বা আইনগুলি ততটা মান্য করে না। বরং অমান্য করতেই মানুষ উদগ্রীব। অ-মান্য করে ধরা পরলে তা থেকে রেহাই পাওয়ারও নানারকম ফন্দিফিকির বের করা হয়।
মনুসংহিতায় বলা হয়েছে– “তস্মাদ্ধর্মং যমিষ্টেষু স ব্যবসেন্নরাধিপঃ”। অর্থাৎ শিষ্টের পালন এবং দুষ্টের দমনের জন্য ধর্মের যে ব্যবস্থা করা আছে, রাজা যেন সেই ধর্মের ব্যবস্থা করেন এবং তা থেকে বিচ্যুত না হন। প্রাচীনকালে যিনিই রাজা, তিনিই দণ্ডদাতা। ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ (আইন বিশেষজ্ঞও বটে) মেধাতিথি বলেছেন – পূর্বতন শাস্ত্র ও সামাজিক আচারের অবিরুদ্ধ যে নিয়মকানুন, রাজা সেগুলোর ব্যবস্থা করবেন– “কার্যব্যবস্থাং শাস্ত্রাচারবিরুদ্ধা”। দণ্ড কেমন দেখতে? মনু তারও বর্ণনা দিয়েছেন– এক ঘোর কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ। তাঁর চোখ দুটি ক্রোধে রক্তিম।
দণ্ডের কেন প্রয়োজন? (১) ভয়ংকর দণ্ডের উপস্থিতিতে শৃঙ্খলা ভাঙার প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করে এবং (২) দণ্ড হবে এমন ভয় যদি প্রতিরোধক হিসাবে কাজে না-দেয়, তখন অপরাধের তারতম্য অনুসারে দণ্ড প্রয়োগ করতে হবে। মনু দণ্ডের চারটি পর্যায় নির্ণয় করেছেন। সেগুলির মধ্যে চরমতম হল মৃত্যুদণ্ড। মৃত্যুদণ্ডের আবার দুটি মানদণ্ড। অব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে একরকম, ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে অন্যরকম। অর্থাৎ একই ধরনের অপরাধে শূদ্রের যেখানে মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত, সেখানে ব্রাহ্মণ হলে মৃত্যুদণ্ড হবে না। ব্রাহ্মণ যদি সত্যিই তেমন অপরাধ করে ফেলেন, তখন তাঁকে মস্তকমুণ্ডন করে দেওয়া বা নির্বাসনে পাঠাতে পারেন রাজা। কিন্তু কখনোই কোনো অপরাধেই ব্রাহ্মণকে হত্যা করা যাবে না। হত্যা করা তো দূরের কথা, ব্রাহ্মণকে হত্যা করব এমন ভাবাটাও রাজা বা দণ্ডদাতার জন্য পাপ। অবশ্য বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা অনুযায়ী একই অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হতে পারে ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র সকলেরই। রায়দানকালে কে ব্রাহ্মণ কে শূদ্র দেখার নিয়ম নেই।
কৌটিল্যের যুগে চার ধরনের অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল– (১) রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গুপ্তচর বৃত্তি, (২) রাষ্ট্রের সম্পত্তি, রাজার ব্যক্তিগত ধন চুরি, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, (৩) নৃশংস কোনো অপরাধ এবং (৪) অপহরণ ও ধর্ষণ, ব্রাহ্মণ নারীর সঙ্গে শূদ্রের যৌনসম্পর্ক এবং তীর্থস্থানে চুরি, ডাকাতি ইত্যাদি।
শুধু প্রাচীন যুগেই নয়, মধ্যযুগেও মৃত্যুদণ্ড বহাল ছিল। ভারতের মধ্যযুগে, অর্থাৎ সুলতান ও মোগল যুগে অনেকক্ষেত্রেই লিখিত কোনো আইন ছিল না। সেসময় সুলতান বা শাসকের ইচ্ছাই চূড়ান্ত। কারণ তিনিই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। মূলত ইসলামী আইন তথা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত বিধান অনুসারেই শাস্তি প্রদান করা হত। “আইন-ই-আকবরী গ্রন্থ থেকে জানা যায়, বাংলার গৌড় দুর্গের উত্তরে কয়েক মাইল দূরে বিশাল বাড়ি জলাধার ছিল। আর সেই জল ছিল বিষাক্ত। মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীদের সেখানে বন্দি অবস্থায় রাখা হত। তৃষ্ণার্ত বন্দিরা সেই বিষাক্ত জলাশয়ের জল পান করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ত। আকবর অবশ্য এই ধরনের মৃত্যুদণ্ড বাতিল করেছিলেন। বাতিল করেছিলেন আরও এক ধরনের নিষ্ঠুর মৃত্যুদণ্ড, যেক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত অপরাধীকে জীবন্ত অবস্থায় গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া হত। সম্রাট জাহাঙ্গিরের আত্মজীবনী ‘তুজুক-ই-জাহাঙ্গির’ থেকে জানা যায়, তিনি ৭০০ জন বিশ্বাসঘাতককে জীবন্ত অবস্থায় শূলে চড়িয়ে হত্যা করেছিলেন। এই ব্যবস্থায় অপরাধীরা তিল তিল করে মরত। প্রতিপালকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে কেমন হতে পারে, তার ভয় দেখানো। এছাড়া প্রকাশ্য দিবালোকে হাজার হাজার সাধারণ মানুষের সামনে অপরাধীদের নৃশংস মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হত, যাতে মৃত্যুর আতঙ্ক সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে Manrique নামে এক পর্যটক এসে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যেসব গাছে ফল ফলত না, সেইসব গাছে চোর-ডাকাতের ঝুলন্ত মৃতদেহ।
ভারতে কোম্পানি যুগে এবং ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড বহাল ছিল। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের আগে পর্যন্ত ভারতের বিদ্যমান ফৌজদারি আইনগুলিকে লর্ড ম্যকলে অ্যাংলো-মুসলমান নির্মাণ বলে চিহ্নিত করেছেন। তবে ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তী কোম্পানির প্রণীত ফৌজদারি আইন কোনো ব্যক্তির জীবন কেড়ে নেওয়ার বৈধতা দিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকে। যদিও আরও আগে, ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস আদেশ দিয়েছিলেন ডাকাতদের প্রকাশ্যে নিজেদের গ্রামে ঝুলিয়ে ফাঁসি দেওয়া হবে। আজও গ্রামে ‘ফাঁসিতলা’ নামে জায়গার বা অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়। ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দে ‘কোর্ট অব ডিরেক্টরস’ প্রাণ কেড়ে নেওয়ার পর মৃতদেহ প্রকাশ্যে ঝুলিয়ে রাখা নিষিদ্ধ করে দেয়। ম্যাকলে ছিলেন মৃত্যুদণ্ডের ঘোরতর সপক্ষে। ভারতেও ম্যাকলে, মিলেট ও ম্যাকলিয়ড এই তিনজন মিলে চার বছর ধরে কঠোর পরিশ্রম করে ভারতীয় দণ্ডবিধির খসড়া প্রস্তুত করেন। ১৮০৮ সালে ইংল্যান্ডে মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকবে কি থাকবে না তা নিয়ে তুমুল বিতর্ক হয়। ছোটোখাটো অপরাধেও মৃত্যুদণ্ড হত। আক্ষরিক অর্থেই লঘুপাপে গুরুদণ্ড আর কি। মুরগি চুরি করলেও চোরের ফাঁসি হত। সেই আইন বাতিল করার লক্ষ্যে ‘রোমিলি বিল’ পেশ করা হয়। অবশেষে ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে ‘রোমিলি বিল’ পাশ হলে চুরির দায়ে চোরের ফাঁসি বাতিল হয়।
১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের পর ভারতে ম্যাকলে প্রণীত ভারতীয় দণ্ডবিধির (IPC) প্রয়োগ শুরু হল। যদিও ভারতীয় এই দণ্ডবিধি চালু হওয়ার কথা ছিল ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ১ মে, কিন্তু চালু হল ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি। ম্যাকলে প্রণীত ইন্ডিয়ান পেনাল কোডে সাতটি প্রধান অপরাধের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড বিধান রেখেছিলেন। তবে বিকল্পে যাবজ্জীবনের ব্যবস্থাও রেখেছিলেন। আমরা এবার দেখে নেব সেই সাতটি প্রধান অপরাধ কেমন। (১) রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা, বিদ্রোহে মদত। (২) কারোকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জন্য মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। (৩) হত্যা। (৪) যাবজ্জীবন কয়েদি দ্বারা হত্যা (৩০২ ধারা)। (৫) অপ্রাপ্তবয়স্ক বা উন্মাদকে প্ররোচনা অথবা মদত দেওয়া। (৬) ডাকাতি ও হত্যা। (৭) যাবজ্জীবন কয়েদি দ্বারা হত্যা (৩০৭ ধারা)। ম্যাকলের এই কোডের অনুশাসনে কত যে লক্ষ লক্ষ সামাজিক অপরাধী তথা সশস্ত্র বিপ্লবীদের ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল তার একটা সম্পূর্ণ তালিকা আজও করে ওঠা সম্ভব হয়নি। অষ্টাদশ, উনবিংশ, বিংশ শতাব্দীর ভারতের মৃত্যুদণ্ডের ইতিহাসকে মনে করিয়ে দেয় আন্দামান সেলুলার জেল এবং তার ফাঁসির মঞ্চ। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহি বিদ্রোহের পর ব্রিটিশরা ভারতীয় বিদ্রোহীদের কামানের মুখে বেঁধে উড়িয়ে দিত। কিন্তু কামানের গোলা কতজনকে ওড়ানো সম্ভব! তাছাড়া কামানের গোলা-বারুদের খরচও বিস্তর। এদিকে টেলিগ্রাফ পোস্টে বিদ্রোহীদের ফাঁসি দিয়ে টাঙিয়ে রাখতে রাখতে ব্রিটিশরা ক্লান্ত। প্রকাশ্যেই সেসব ফাঁসি দেওয়া হত। পাছে এসব দেখে মানুষ যদি ক্ষেপে যায়, সেই কারণে জনসাধারণের চোখের আড়ালে নিভৃতে হত্যা করাই কাম্য। অতএব বাকি বিদ্রোহীদের আন্দামানে পাচার। এখানে সারা বিশ্বের চোখের আড়ালে কয়েদি তথা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর নির্মম অত্যাচার করা ছিল সহজ। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিলে ২৩৮ জন করাবন্দি জেল থেকে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। তাঁদের মধ্যে ৮৭ জনকে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়। ফাঁসি হয় রস আইল্যান্ডের গভীর অরণ্যে। বাকিদের পরিণতি আলাদা করে বলার কিছু নেই। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে বড়োলাট লর্ড মেয়ো আন্দামান পরিদর্শনে এসেছিলেন। সুযোগ বুঝে শের আলি লর্ড মেয়েকে হত্যা করেন। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দের ৮ ফেব্রুয়ারি শের আলির ফাঁসির গলায় পরে শহিদ হন। পোর্ট ব্লেয়ারের পাশে ভাইপার দ্বীপের জেলে এই ফাঁসি কার্যকর করা হয়। মাত্র ৩ বছর সময়ের মধ্যেই সেই কুখ্যাত সেলুলার জেলটি নির্মিত হয়েছিল ৬০০ কয়েদির রক্ত-ঘাম ঝরিয়ে দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রমে। শের আলিই প্রথম কয়েদি, যিনি আন্দামানের প্রথম শহিদ। মনে রাখতে হবে যে, সেলুলার জেলে শুধু রানৈতিক বন্দিদেরই রাখা হত না, রাখা হত অন্যান্য বন্দিদেরও। মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত সেইসব বন্দিদের সেলুলার জেলের ফাঁসিঘরে ফাঁসি দেওয়া হলেও কোনো রাজনৈতিক বন্দিদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছে বলে কোনো নথি পাওয়া যায় না।
যেভাবেই হোক অবশেষে ভারত ব্রিটিশমুক্ত হল। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। কিন্তু তথাকথিত এই স্বাধীন ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক যুগের রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতিগুলো সরাসরিভাবে উত্তর-ঔপনিবেশিক যুগে স্থায়ী রূপ নিল। অপরিবর্তিতই থেকে গেল আমলাতন্ত্র, পুলিশী ব্যবস্থা ও মিলিটারি কাঠামো। ফৌজদারি, দেওয়ানি আইনের বিশেষ কোনো পরিবর্তনই হল না। বহাল থাকল মৃত্যুদণ্ডও। পরিবর্তন যে কিছু হয়নি, তা অবশ্য বলা যায় না। যেমন ধরুন, ১৮৯৮ সালের যে কার্যবিধি অনুসারে হত্যার ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড দেওয়াটাই ছিল বাধ্যতামূলক, আর ব্যতিক্রম ছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ড– সেই কার্যবিধি ১৯৫৫ সালে আইন সংশোধন করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল নিয়ম, মৃত্যুদণ্ড হল ব্যতিক্রম। ১৯৮৩ সালের ৭ এপ্রিল থেকে ম্যাকলের ৩০৩ ধারা বাতিল হয়ে যায়। কারণ এই ধারায় মৃত্যুদণ্ড ছিল বাধ্যতামূলক।
ভারতে মৃত্যুদণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি পি এন ভাগবতী স্পষ্টভাবে বললেন– মৃত্যুদণ্ড ভারতীয় সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদের (জীবনের অধিকার) পরিপন্থী। মৃত্যুদণ্ড তাই সংবিধান বিরোধী। মাননীয় বিচারপতির যুক্তি– (১) সংবিধানে সবিস্তারে বলা নেই যে, মৃত্যুদণ্ড নিষিদ্ধ। কিন্তু জীবনের অধিকারের ধারণা, রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালের ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতা একটি ধারণাই প্রতীয়মান করে যে, মৃত্যুদণ্ড বিরোধী প্রবণতার দিকেই পাল্লা ভারী। তাঁর ভাষায়– “The legislative amendments, has shifted the punitive centre of gravity from life to life sentence.” (২) মৃত্যুদণ্ড সম্পূর্ণভাবে অ-পরিবর্তনযোগ্য (irrevocable/irreversible)। যতদিন মৃত্যুদণ্ড প্রথা থাকবে, ততদিন আদালতের পূর্ণ সম্ভাবনা থাকবে নির্দোষ ব্যক্তির প্রাণ নিয়ে নেওয়ার। (৩) বিগত ১৫০ বছরের ইতিহাসে দেখাতে পারেনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের তুলনায় মৃত্যুদণ্ড অনেক বেশি প্রতিরোধক হিসাবে কার্যকর। (৪) এই প্রথা স্বেচ্ছাচারমূলক ও অযৌক্তিক এবং তাই ভারতীয় সংবিধানের ১৪ এবং ২১ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘনকারী। (৫) মৃত্যুদণ্ডের প্রশ্নে বিচারপতির ‘discretion’ থাকার অর্থ বিচারপতির ভাবাদর্শ, মূল্যবোধের উপর একজনের যাবজ্জীবন বা মৃত্যুদণ্ড নির্ভর করবে। (৬) প্রাণদণ্ডের শ্রেণিচরিত্র আছে। গরিব ও অবহেলিত মানুষরাই এর শিকার হয়।
এ প্রসঙ্গে বিচারপতি কৃষ্ণ আয়ার বচন সিং মামলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতকে ‘rarest of rare cases’ বা Judicial gamble’ বা বিচারবিভাগীয় জুয়াখেলা আখ্যা দিয়েছেন। হেতাল পারেখ মামলায় ধনঞ্জয়ের মৃত্যুদণ্ড এমনই এক জুয়াখেলার শিকার বলে মনে করেন বিদগ্ধজনেরা। এই রায় দিতে গিয়ে আদালত বলেছিল— ‘rarest of rare cases’। সেই বিচার, সেই মৃত্যুদণ্ডের রায় যে ভুল ছিল তার ব্যাখ্যা দিয়ে দেবাশিস সেনগুপ্ত, প্রবাল চৌধুরী পরমেশ গোস্বামী রচিত “আদালত, মিডিয়া, সমাজ এবং ধনঞ্জয়ের ফাঁসি’ শিরোনামে একটি তথ্যসমৃদ্ধ বই প্রকাশিত করে। এমনকি এই বিতর্কিত মৃত্যুদণ্ড নিয়ে পরিচালক অরিন্দম শীল ‘ধনঞ্জয়’ নামে একটি সিনেমাও করলেন। ১৯৯০ সালে এক কিশোরীকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ ওঠে ধনঞ্জয়ের বিরুদ্ধে। ১০ বছর কারাবাসের পর ২০০৪ সালে তাঁর ফাঁসি হয়। তখন থেকেই উঠেছে প্রশ্ন। অনেকেই বলেন, ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় যে মামলায় অভিযুক্ত প্রমাণিত হয়েছেন, তার বহু কিছুই পোয়াঁশায় ভরা, বহু ‘প্রমাণ’ মূলত গোঁজামিল। এমনকি সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ জড়ো করে এগোলে ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়ের ঘটানো ‘অপরাধ’ আদৌ প্রমাণ করা যায় কি না, এ নিয়েই সন্দেহ তৈরি হয়। এমনকি ওই সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে ভিন্নতর সিদ্ধান্তে পৌঁছনোও সম্ভব ছিল বলে দাবি ওঠে। বিচারে বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদলে, সেই কান্না শুনবে কে?
ধনঞ্জয়ের ফাঁসি ভুল ছিল কি ঠিক ছিল, সেই বিচার করা আজ আর কোনো মানে রাখে না। যদি ভুল হয়, তাহলে তাঁকে তো আর পুনর্জীবন দেওয়া সম্ভব নয়! মানুষ কেবল হত্যা করতে পারে, কিন্তু প্রাণ ফিরিয়ে দিতে অক্ষম। হেগেল তাঁর উপযোগবাদের শাস্তির তত্ত্বে বলেছেন, “শান্তি মানে ভুলের বাতিল (annulment of wrong)”। অর্থাৎ যা ঘটে গেছে, যাকে হত্যা করা হয়েছে তাঁকে কী ফিরিয়ে আনা যাবে? হেগেলের মতে, শাস্তি মানে যন্ত্রণা ভোগ করার জন্য দৈহিক নির্যাতন। তাই যদি হয় এবং নির্যাতিত বা অপরাধের পক্ষে যদি ন্যায় বিচার দিতে হয় তাহলে তা হত্যার বদলে হত্যা। এই ধরনের হত্যাকে বলা হয় রাষ্ট্র কর্তৃক একটি হোমিসাইড। রাষ্ট্র বারবার সেই ধরনের হত্যাকেই সবচেয়ে ভয়ংকর বলেছে যা পূর্বপরিকল্পিত, যাকে বলা হয় ঠান্ডা মাথায় খুন এবং একটি প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতির মাধ্যমে তার সমপরিমাণে যোগ্য শাস্তি হল আর-একটি হত্যা। তাই নয়কি? যে নৈতিকতার মানাঙ্কে একজন অপরাধী ব্যক্তিকে রাষ্ট্র মৃত্যুদণ্ড দিচ্ছে, সে নিজেও সেই নৈতিকতার মানাঙ্কে ঠান্ডা মাথায় পূর্বপরিকল্পিতভাবে দিনক্ষণ পদ্ধতি নির্দিষ্ট করে হত্যা করছে। ক্যামুর ভাষায়– “The death penalty … usurps as exorbitant privilege by claiming to punish an always relative culpability by a definitive and irrepairable punishment.”
প্রাক্তন বিচারপতি ও মানবাধিকার আন্দোলনের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব রাজেন্দ্র সাচার মনে করেন– বিরলতম ঘটনায় মৃত্যুদণ্ডের কথা সুপ্রিম কোর্ট বললেও যেহেতু কোনো মানদণ্ড নেই, সেহেতু বিচারপতিরা নিজেদের ভাবাদর্শ ও মূল্যবোধ অনুসারে বিরলতম নির্ধারণ করছেন ও যথেচ্ছাচারভাবে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দিচ্ছেন। মাননীয় সাচার একটি পরিসংখ্যান পেশ করে বলেছেন– ১৯৭০ থেকে ১৯৮০ এই দশ বছরে সুপ্রিম কোর্ট ৩৭.৭ শতাংশ মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করেছিল। ১৯৯০ দশক জুড়ে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪০ শতাংশ। হাইকোর্টের ক্ষেত্রে ১৯৮০ দশকে শতকরা ৫৯ ভাগের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা হত। ১৯৯০ দশকে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬৫ শতাংশ।
মানবসমাজে অপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি Capital Punishment হিসাবে বহুকাল আগে থেকেই প্রচলিত মৃত্যুদণ্ড। সর্বোচ্চ শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ড প্রথম কার্যকর করা হয় মিশরে খ্রিস্টপূর্ব ষোলো শতকে। তখন কুঠার দিয়ে মুণ্ডচ্ছেদ করা হত। ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনে সাধারণ অপরাধের জন্যও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া। হত। খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ খ্রিস্টাব্দে কাদার মধ্যে পুঁতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করত ব্রিটিশরা। ১৫৩১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটেনে নতুন আইনে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় জীবন্ত সিদ্ধ করে। ব্রিটিশ আমেরিকান কলোনীতে ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে প্রথম মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় ভার্জিনিয়ার জর্জ কেল্ডাবালাকে। ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে টেক্সাসে প্রথম বিষাক্ত ইনজেকশন পুশ করে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। এখন দেখি কোন্ দেশে কী ধরনের মৃত্যুদণ্ডের প্রচলন আছে।
(১) শিরচ্ছেদ– সৌদি আরব, কাতার। (২) ইলেকট্রিক চেয়ার– আমেরিকা, ফিলিপাইন। (৩) ধাক্কা মেরে পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া– ইরান, চিলি। (৪) গ্যাস চেম্বার– আমেরিকা। (৫) ফাঁসি– আমেরিকা, আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, মঙ্গোলিয়া, জাপান, পাকিস্তান, ভারত, মিশর, ফিলিপনস, সিঙ্গাপুর, লাইবেরিয়া, কোরিয়া, বাংলাদেশ সহ অনেক দেশে। (৬) ইনজেকশন– আমেরিকা, ফিলিপিনস, গুয়েতমালা, থাইল্যান্ড, চিন, তাইওয়ান, ভিয়েতনাম। (৭) ফায়ারিং স্কোয়াড– আমেরিকা, চিন, ভিয়েতনাম, রাশিয়া, লেবানন সহ অনেক দেশে। (৮) ছুরিকাঘাত— সোমালিয়া ইত্যাদি।
শুধু সেই রাষ্ট্রের বিচার-ব্যবস্থাই নরহত্যায় সামিল হয় তা নয়, রাষ্ট্রের যন্ত্র তথা পুলিশ মায় প্রতিরক্ষা বাহিনীর সমস্ত শাখাই নরহত্যা করে থাকে নির্বিচারে। পুলিশী হেফাজতে কত অভিযুক্তকে বিচারের আগে মেরে ফেলা হচ্ছে, তার হিসাব কে রেখেছে! সেনাবাহিনীর কর্মীরাও বহু ক্ষেত্রেই বিনা প্ররোচনায় মানুষ হত্যা করে থাকে। সেইরকমই এক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আজও দীর্ঘপ্রায় ১২ বছর ধরে শর্মিলা চানু অনশন চালিয়েছিল।
থানা, অর্থাৎ পুলিশ স্টেশনের কাছাকাছি যাঁদের বাড়ি তাঁদের প্রত্যেরই নিশ্চয় পুলিসের হেফাজতে থাকা ধৃত ব্যক্তির আর্তনাদ শোনার অভিজ্ঞতা হয়েছে। তারপর পরের দিন সকালে খবরের কাগজে পুলিশের বয়ানে আষাঢ়ে গল্পও পড়েছেন। আষাঢ়ে গল্প এক : ধৃত ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে। আষাঢ়ে গল্প দুই : এনকাউন্টারে মৃত্যু। সবাই যে এ ঢপের গপ্পো বিশ্বাস করে তা নয়। ফলে তাঁরা ঘেরাও করে, ওসির শাস্তির দাবি করে। দু-চারদিন সেই প্রতিবাদের থাকে। তারপর সব শান্ত, যেন কিছুই হয়নি। অজানা থেকে যায় অত্যাচারী খুনী পুলিশের শাস্তি হল কি না। সকলের কাছে এটাই স্বাভাবিক বলে মনে হয় যে, পুলিশ ধৃত ব্যক্তিকে মারধোর করবেই এবং তা অবশ্যই আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার স্বার্থে। তাই বলে মেরে ফেলবে ধৃত ব্যক্তিকে, তাও বিনা বিচারে? পুলিশ মৃত্যুদণ্ড দিতে পারে? পুলিশের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অধিকার আছে? প্রশ্ন অনেক হলেও উত্তর একটাই : না। কারণ আইনের রক্ষক পুলিশ বাহিনীও আইনের অধীন। মূলত দুটি আইনের সাহায্যে পুলিশ ‘শান্তি-শৃঙ্খলা’ বজায় রাখে। (১) ভারতীয় দণ্ডবিধি বা ইন্ডিয়ান পেনাল কোড ও (২) সংশোধিত ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ বা ক্রিমিন্যাল প্রসিডিওর কোড। এই আইনে ধৃত ব্যক্তির উপর নির্যাতনের কোনো অধিকার দেওয়া হয়নি পুলিশকে, কোনো অবস্থাতেই নয়। তা সত্ত্বেও পুলিশ ধৃত ব্যক্তিকে যথেষ্ট বলপ্রয়োগ ও মারধোর করে। ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩৩০, ৩৩১ ধারায় ও ফৌজদারি কার্যবিধি ১৯৭ ধারায় পুলিশের বিরুদ্ধে শাস্তির বন্দোবস্ত করা আছে। অপরাধ স্বীকৃতি আদায়ের জন্য শারীরিক আঘাত বা ক্ষত সৃষ্টি করা পুলিশের অপরাধ। সেক্ষেত্রে পুলিশের সাত বছর কারাদণ্ড হতে পারে। ধৃত ব্যক্তি যদি গুরুতর আহত হন তাহলে সেক্ষেত্রে দশ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। আবার শারীরিক নির্যাতন না করেও যদি নির্যাতনের ভয় দেখানো হয়, তাহলে সেটাও নির্যাতন করার অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের ২০ তারিখে রাষ্ট্রপুঞ্জের পৃষ্ঠপোষকতায় জেনেভায় অনুষ্ঠিত মানবাধিকার কমিশনের ৪৫ তম অধিবেশনে ভারত সরকারের প্রতিনিধি ও সংসদ সদস্য এস এস আলুওয়ালিয়া তাঁর ভাষণে বলেন –”নিপীড়ন হচ্ছে সবচেয়ে জঘন্যতম মানবাধিকার লঙ্ঘন। আমরা এও মনে করি যে, নিপীড়নের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। বিরোধী কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করার জন্য এই ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়, যা সাংবিধানিক সমানাধিকারকে লঙ্ঘন করে। জঘন্যতম অত্যাচারগুলি সংঘটিত হয় টর্চার সেলে বা জেলখানায় … ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অথবা বাঁচার অধিকার ভারতীয় সংবিধানে সকল নাগরিককে অর্পণ করেছে … ভারতের আইনবিধিতে পুলিশ কর্তৃক ধৃত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটানোর ক্ষমতা দেওয়া হয়নি। পলায়নরত অথবা বাধাদানকারী ধৃত ব্যক্তিকেও পুলিশ হত্যা করতে পারে না। … জেরার সময় বন্দি ধৃতের উপর পুলিশ অফিসার থার্ড ডিগ্রি’ পদ্ধতি গ্রহণ না করে তার জন্য বিভিন্ন সময়ে ভারত সরকার নির্দেশ দিয়েছে।”
শুধু আইন নয়, সারা বিশ্বের কাছে ভারত সরকার ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ১০ ডিসেম্বর রাষ্ট্রসংঘের দফা মানবাধিকার সনদে স্বাক্ষর করে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে, সেই সনদের ৫ ধারা (“No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.”) অনুসারে ভারতে কোনো বন্দিকে কোনো ধরনের নির্যাতন করা সম্পূর্ণভাবে বেআইনি ও মানবাধিকার লঙ্ঘন। মনে রাখা প্রয়োজন, নির্দিষ্ট বিধি মেনে পুলিশ কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা মানেই সে ‘দোষী’ বা ‘অপরাধী’ নয়। যতদিন-না পর্যন্ত আদালতে ধৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ পুলিশ প্রমাণ করতে পারছে, ততদিন পর্যন্ত ধৃত ব্যক্তি নিরপরাধ এবং সেই নিরপরাধকে অত্যাচার করা সর্বাধিক ১৫ দিনের পুলিশ হাজতে শুধু বেআইনি নয়, তাঁর ব্যক্তিসত্তার উপর চরমতম আঘাত। কারণ পুলিশ সাজা দেওয়ার অধিকারী নয়। সাজা দেওয়ার একমাত্র অধিকার আছে আদালতের।
কলকাতার টালিগঞ্জে ‘রিট্রিট’ নামে একটি অত্যাচার গৃহ আছে। খোদ লালবাজার সহ ভারতের সর্বত্র থানা লক আপে পুলিশ কর্তৃক ধৃতদের উপর বীভৎস অত্যাচার চলে। নানা কায়দায় নির্যাতন করে বহু ধৃত ব্যক্তিকে। অমানুষিক অত্যাচারের ফলে ধৃতব্যক্তি মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা ট্রেনিং স্কুলে পুলিশ প্রশিক্ষণের সময় থার্ড ডিগ্রি’ কায়দায় অত্যাচারের যে ফিরিস্তি পেশ করা হয়েছে, তা জানলে শিউরে উঠতে হয়। এলোপাথারি মারধোর করা, শরীরে সিগারেটের ছ্যাঁকা দেওয়া, খাবার ও জল না দেওয়া এবং ঘুমোতে না দেওয়া, পেচ্ছাব খেতে বাধ্য করা, ইলেকট্রিক শক দেওয়া, উলঙ্গ করিয়ে ভিড় রাস্তা দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া, বাঁশকল করে মাথা নিচু করে ঝুলিয়ে আগাপাশতলা ডাণ্ডা দিয়ে পেটানো, দু-পায়ে দড়ি বেঁধে মাথা নিচের দিক করে দীর্ঘক্ষণ ঝুলিয়ে রাখা, গরম জলের বোতল দিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া, হাত-পা বেঁধে পাজামার ভিতর আরশোলা বা ইঁদুর ঢুকিয়ে দেওয়া, দু-পায়ে দড়ি বেঁধে মাথা নিচের দিক করে দীর্ঘক্ষণ ঝুলিয়ে রাখা অবস্থায় মাথা বস্তা বেঁধে দেওয়া হয় এবং বস্তার ভিতর জ্যান্ত ইঁদুর বা আরশোলা ছেড়ে দেওয়া হয়, মলদ্বারের ভিতর কাঠি বা বিদ্যুত্বহী তার ঢুকিয়ে দেওয়া, দাড়ি বা চুল উপড়ে ফেলা, এক পায়ে এক হাত তুলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রাখা, ইংরেজি Z-এর মতো ত্রিভঙ্গ অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা হামাগুড়ি দেওয়ানো, ধৃত বন্দির শরীরে পেট্রোল অথবা কেরোসিন অথবা অ্যাসিড সিরিঞ্জ দিয়ে পুশ করা ইত্যাদি। এইরকম অমানুষিক অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অনেক ধৃত ব্যক্তি মারা যান। ধৃত ছেড়ে দেওয়ার বাহানা করে মাঝরাতে লকআপ থেকে বের করে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে গুলি মেরে ফেলার অভিযোগও পুলিশের বিরুদ্ধে আছে।
এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এ এন মোল্লা ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে জনৈক পুলিশ অফিসার নঈমের বিরুদ্ধে জনৈক ভারতীয় নাগরিকের মামলার রায়ে বলেছিলেন : “সমস্ত দায়িত্ব নিয়েই আমি একথা বলতে পারি যে, সারা দেশে এমন কোনো গোষ্ঠী নেই যাঁদের অপরাধের খতিয়ান ধারে কাছেও যেতে পারে সেই সংগঠিত গুণ্ডাবাহিনীর, যার নাম কিনা ভারতীয় পুলিশ বাহিনী।”
পুলিশ মানুষ হত্যা করে। অসহায় ধৃতদের নির্বিবাদে হত্যা করে। বিচারে ধৃতের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণ হওয়ার আগেই হত্যা করে। বস্তুত ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর কাছে ক্ষমতা বুঝে নেওয়ার পরে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ‘লৌহমানব’ বল্লভভাই প্যাটেল উচ্চকিত কণ্ঠে বলেছিলেন– “এতদিন আমরা যে পুলিশ বাহিনীর সমালোচনা করেছিলাম, সে অন্য পুলিশ। আর এখনকার পুলিশ হল স্বেচ্ছাসেবক…”। তারপর অনেক জল গড়িয়ে গেছে গঙ্গা-যমুনা কৃষ্ণা-গোদাবরী দিয়ে। ভারতের অন্য রাজ্যের কথা কথা তো বাদই দিলাম। শুধু পশ্চিমবঙ্গেই খুনি পুলিশবাহিনীদের ট্র্যাক রেকর্ড দেখলে চমকে যেতে হয়।
যত দিন যাচ্ছে ‘স্বাধীন’ রাষ্ট্রের পুলিশের নিশানা ততই অব্যর্থ হয়ে উঠছে। মাথা, বুক, পেট ভেদ করে তপ্ত সিসা অনেকদিন আগেই জানিয়ে দিয়েছে– প্রতিবাদ করলেই মৃত্যু, অধিকারের কথা বললেই বিচ্ছিন্নতাবাদী, মুখ খুললেই দেশদ্রোহিতা। অতএব চুপ করে থাকো সবাই। কথা বললেই গুম। বিরোধিতা করলেই বিনাশ। অনুগত হও। অনুগত হও। অনুগত হও। বেগড়বাই করলেই রাষ্ট্রের অঙ্গুলি হেলনে অন্তরীণ। গণতন্ত্রে মানুষের কথাই শেষ কথা, মানুষের হৃদয়ের ভাষাই রাষ্ট্রের ভাষা– এই পরম সত্যটিকে বিদ্রূপ করতেই যেন পুলিশের কথাই শেষ কথা। পুলিশ-হাজতে বা তত্ত্বাবধানে ধৃত ব্যক্তিদের মৃত্যুর সংখ্যা যেভাবে বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে, তা মানবসভ্যতার অপমৃত্যুকেই ডেকে আনছে।
১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১০ নভেম্বর। স্বাধীন রাষ্ট্রের বয়স তখন মাত্র তিন মাস। আমরা সেদিন প্রথম বুঝলাম শাসক বিদেশি না স্বদেশি সেটা কোনো বিষয় নয়– শাসক শাসকই হয়। বিদেশিই হোক অথবা স্বদেশি– আসল বিষয় ছলে-বলে-কৌশলে ক্ষমতার হস্তান্তর। ব্রিটিশদেরই তৈরি ‘স্পেশাল পাওয়ার বিল’ (এ বিল মানুষকে অবাধে খুন করার বিল বা ছাড়পত্র প্রত্যাহারের দাবিতে মিছিল বের করেছিল একদল ভারতীয় নাগরিক ভারতের মাটিতেই। সম্পূর্ণ নিরীহ ওই মিছিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল স্বাধীন ভারতের স্বদেশি পুলিশের গুলি। অকুস্থলে লুটিয়ে পড়ল আরডব্লিউএসির স্বেচ্ছাসেবক জনৈক শিশির মণ্ডল। স্বাধীন দেশের স্বদেশি পুলিশের বন্দুকবাজির প্রথম শিকার। ১৯৫৯ এবং ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতবাসী দু-দফায় খাদ্য আন্দোলনে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ভংয়কর দানবীয় রূপ প্রত্যক্ষ করেছিল। এ বছরেই তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে দশ হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রীর এক বিশাল মিছিলের উপর পুলিশের গুলি চালায়। নির্বিচারে এই গুলি বর্ষণে মৃত্যু হয় ১১ জনের। ৩ সেপ্টেম্বর আবার গুলি চলল কলকাতা, হাওড়া ও ২৪ পরগনায়– মৃত্যু হল ১৫ জনের। পরের দিন আবার গুলিবর্ষণ। মৃত্যু হল ১০ জনের। সব মিলিয়ে এক সপ্তাহে পুলিশ হত্যা করেছিল প্রায় ৮০ জনকে।
এলো ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দ। তৎকালীন মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙারের জ্ঞাতসারে যুক্তফ্রন্টের পুলিশ গুলি চালিয়ে সাতজন কৃষক মহিলাকে হত্যা করল। এদের মধ্যে একজনের পিঠে বাঁধা ছিল এক দুধের শিশু। পুলিশের গুলি মাকে হত্যা করে শিশুটিকেও এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছিল। সত্তর দশকে শুধুমাত্র কলকাতার বুকেই ১৭৮৩ জন যুবককে হত্যা করেছিল পুলিশ। সে সময় নকশাল মানেই সে বধযোগ্য। এনকাউন্টার’-এর নামে পুলিশ ঠান্ডা মাথায় হাজার হাজার যুবককে হত্যা করেছিল। সত্তরের দশক ছিল নরমেধ যজ্ঞের দশক। পুলিশের গুলিতে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছিল এক সম্ভাবনাময় তরুণ প্রজন্মকে। মরিচঝাঁপির নিরীহ অসহায় মানুষদের পুড়িয়ে গণহত্যা, আনন্দমার্গীদের গণহত্যা, নন্দীগ্রামের গণহত্যার ঘটনাগুলির মতো এরকম অজস্র ঘটনা আছে, সেগুলি পরপর সাল-তারিখ দিয়ে আলোচনা করলে একটা গোটা মহাভারতে আঁটবে না।
সুপ্রিমকোর্ট ধৃতের উপর পুলিশের অত্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর একটি G|Sacri Chai Shri D.K. Basu,Ashok K. Johri vs State Of West Bengal,State Of U.P on 18 December, 1996 Oulfat moacha জ্ঞাতব্যের জন্য হুবহু তুলে ধরলাম।
WITH WRIT PETITION (CRL) NO. 592 OF 1987 JUDGMENT DR. ANAND, J.
The Executive Chairman, Legal Aid Services, West Bengal, a non-political organisation registered under the Societies Registration Act, on 26th August, 1986 addressed a letter to the Chief Justice of India drawing his attention to certain news items published in the Telegraph dated 20, 21 and 22 of July, 1986 and in the Statesman and India express dated 17th August, 1986 regarding deaths in police lock-ups and custody. The Executive Chairman after reproducing the new items submitted that it was imperative to examine the issue in depth and to develop “custody jurisprudence” and formulate modalities for awarding compensation to the victim and/or family members of the victim for attrocities and death caused in police custody and to provide for accountability of the efforts are often made to hush up the matter of lock-up deaths and thus the crime goes unpunished and “flourishes”. It was requested that the letter alongwith the new items be treated as a writ petition under “public interest litigation” category.
Considering the importance of the issue raised in the letter being concerned by frequent complaints regarding custodial violence and deaths in police lock up, the letter was treated as a writ petition and notice was issued on 9.2.1987 to the respondents.
In response to the notice, the State of West Bengal filed a counter. It was maintained that the police was no hushing up any matter of lock-up death and that whereever police personnel were found to be responsible for such death, action was being initiated against them. The respondents characterised the writ petition as misconceived, misleading and untenable in law.
While the writ petition was under consideration a letter addressed by Shri Ashok Kumar Johri on 29.7.87 to the Hon’ble Chief Justice of India drawing the attention of this Court to the death of one Mahesh Bihari of Pilkhana, Aligarh in police custody was received. That letter was also treated as a writ petition and was directed to be listed alongwith the writ petition filed by Shri D.K. Basu. On 14.8.1987 this Court made the following order :
“in almost every states there are allegations and these allegations are now increasing in frequency of deaths in custody described generally by newspapers as lock-up deaths. At present there does not appear to be any machinery to effectively deal with such allegations. Since this is an all India question concerning all States, it is desirable to issues notices to all the State Governments to find out whether they are desire to say anything in the matter. Let notices issue to all the State Governments. Let notice also issue to the Law Commission of India with a request that suitable suggestions may be returnable in two months from today.”
In response to the notice, affidavits have been filed on behalf of the States of West Bengal, Orissa, Assam Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Harayana, Tamil Nadu, Meghalaya, Maharashtra and Manipur. Affidavits have also been filed on behalf of Union Territory of Chandigarh and the Law Commission of India.
During the course of hearing of the writ petitions, the Court felt necessity of having assistance from the Bar and Dr. A.M. Singhvi, senior advocate was requested to assist the Court as amicus curiae.
Learned counsel appearing for different states and Dr. Singhvi, as a friend of the court. presented the case ably and though the effort on the part of the States initially was to show that “everything was well” within their respective States, learned counsel for the parties, as was expected of them in view of the importance of the issue involved, rose above their respective briefs and rendered useful assistance to this Court in examining various facets of the issue and made certain suggestions for formulation of guidelines by this court to minimise, if not prevent, custodial violence and kith and kin of those who die in custody on account of torture.
The Law Commission of India also in response to the notice issued by this Court forwarded a copy of the 113th Report regarding “injuries in police custody and suggested incorporation of Section 114-B in the India Evidence Act.”
The importance of affirmed rights of every human being need no emphasis and, therefore, to deter breaches thereof becomes a sacred duty of the Court, as the custodian and protector of the fundamental and the basic human rights of the citizens. Custodial violence, including torture and death in the lock ups, strikes a blow at the Rule of Law, which demands that the powers of the executive should not only be derived from law but also that the same should be limited by law. Custodial violence is a matter of concern. It is aggravated by the fact that it is committed by persons who are supposed to be the protectors of the citizens. It is committed under the shield of uniform and authority in the four walls of a police station or lock-up, the victim being totally helpless. The protection of an individual from torture and abuse by the police and other law enforcing officers is a matter of deep concern in a free society. These petitions raise important issues concerning police powers, including whether monetary compensation should be awarded for established infringement of the Fundamental Rights guaranteed by Articles 21 and 22 of the Constitution of India. The issues are fundamental.
“Torture” has not been defined in Constitution or in other penal laws. ‘Torture’ of a human being by another human being is essentially an instrument to impose the will of the ‘strong’ over the ‘weak’ by suffering. The word torture today has become synonymous wit the darker side of human civilisation.
“Torture is a wound in the soul so painful that sometimes you can almost touch it, but it is also so intangible that there is not way to heal it. Torture is anguish squeezing in your chest, cold as ice and heavy as a stone paralyzing as sleep and dark as the abyss.
Torture is despair and fear and
rage and hate. It is a desire to
kill and destroy including
yourself.”
—Adriana P. Bartow
No violation of any one of the human rights has been the subject of so many Conventions and Declarations as ‘torture’ all aiming at total banning of it in all forms, but inspite of the commitments made to eliminate torture, the fact remains that torture is more widespread not that ever before, “Custodial torture” is a naked violation of human dignity and degradation with destroys, to a very large extent, the individual personality. IT is a calculated assault on human dignity and whenever human dignity is wounded, civilisation takes a step backward-flag of humanity must on each such occasion fly half-mast.
In all custodial crimes that is of real concern is not only infliction of body pain but the mental agony which a person undergoes within the four walls of police station or lock-up. Whether it is physical assault or rape in police custody, the extent of trauma a person experiences is beyond the purview of law.
“Custodial violence” and abuse of police power is not only peculiar to this country, but it is widespread. It has been the concern of international community because the problem is universal and the challenge is almost global. The Universal Declaration of Human Rights in 1984, which market the emergency of worldwide trend of protection and guarantee of certain basic human rights, stipulates in Article 5 that “No one shall be subjected to torture or to curel, inhuman or degrading treatment or punishment.” Despite the pious declaration, the crime continues unabated, though every civilised nation shows its concern and takes steps for its eradication.
In England, torture was once regarded as a normal practice to ger information regarding the crime, the accomplices and the case property or to extract confessions, but with the development of common law and more radical ideas imbibing human though and approach, such inhuman practices were initially discouraged and eventually almost done away with, certain aberrations here and there notwithstanding. The police powers of arrest, detention and interrogation in England were examined in depth by Sir Cyril Philips Committee- ‘Report of a Royal Commission on Criminal Procedure’ (command– Paper 8092 of 1981). The report of the Royal Commission is, instructive. In regard to the power of arrest, the Report recommended that the power to arrest without a warrant must be related to and limited by the object to be served by the arrest, namely, to prevent the suspect from destroying evidence or interfering with witnesses or warning accomplices who have not yet been arrested or where there is a good reason to suspect the repetition of the offence and not to every case irrespective of the object sought to be achieved.
The Royal Commission suggested certain restrictions on the power of arrest on the basis of the ‘necessity principle’. The Royal commission said :
“… We recommend that detention upon arrest for a offence should continue only on one or more of the following criteria
(a) the person’s’s unwillingness to identify himself so that summons may be served upon him;
(b) the need to prevent the continuation or repetition of that offence;
(c) the need to protect the arrested person’s himself or other persons or property;
(d) the need to secure or preserve evidence of or relating to that offence or to obtain such evidence from the suspect by questioning him; and
(e) the likelihood of the person’s failing to appear at court to answer anycharge made against him.” The Royal Commission also suggested :
“To help to reduce the use of arrest we would also propose the introduction here of a scheme that is used in Ontario enabling a police officer to issue what is called an appearance notice. That procedure can be used to obtain attendance at the police station without resorting to arrest provided a power to arrest exists, for example to be finger printed or to participate in an identification parade. It could also be extended to attendance for interview at a time convenient both to the suspect and to the police officer investigating the case…”
The power of arrest, interrogation and detention has now been streamlined in England on the basis of the suggestions made by the Royal Commission and incorporated in police and Criminal Evidence Act, 1984 and the incidence of custodial violence has been minimised there to a very great extent.
Fundamental rights occupy a place of pride in the India Constitution. Article 21 provides “no person shall be deprived of his life or personal liberty expect according to procedure established by law”. Personal liberty, thus, is a sacred and cherished right under the Constitution. The expression “life of personal liberty” has been held to include the right to live with human dignity and thus it would also include within itself a guarantee against torture and assault by the State or its functionaries. Article 22 guarantees protection against arrest and detention in certain cases and declares that no person who is arrested shall be detained in custody without being informed of the grounds of such arrest and the shall not be denied the right to consult and defend himself by a legal practitioner of his choice. Clause (2) of Article 22 directs that the person arrested and detained in custody shall be produced before the nearest Magistrate within a period of 24 hours of such arrest, excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of the Magistrate. Article 20(3) of the Constitution lays down that a person accused of an offence shall not be compelled to be a witness against himself. These are some of the constitutional safeguard provided to a person with a view to protect his personal liberty against and unjustified assault by the State, In tune with the constitutional guarantee a number statutory provisions also seek to project personal liberty, dignity and basic human rights of the citizens. Chapter V. of Criminal Procedure Code, 1973 deals with the powers of arrest of a person and the safeguard which are required to be followed by the police to protect the interest of the arrested person. Section 41, Cr. P.C. confers powers on any police officer to arrest a person under the circumstances specified therein without any order or a warrant of arrest from a Magistrate. Section 46 provides the method and manner of arrest. Under this Section no formality is necessary while arresting a person. Under Section 49, the police is not permitted to use more restraint than is necessary to permitted to use more restraint than is necessary to prevent the escape of the person. Section 50 enjoins every police officer arresting any person without warrant to communicate to him the full particulars of the offence for which he is arrested and the grounds for such arrest. The police officer is further enjoined to inform the person arrested that he is entitled to be released on bail and he may arrange for sureties in the event of his arrest for a non-bailable offence. Section 56 contains a mandatory provision requiring the police officer making an arrest without warrant to produce the arrested person before a Magistrate without unnecessary delay and Section 57 echoes Clause (2) of Article 22 of the Constituion of India. There are some other provisions also like Section 53, 54 and 167 which are aimed at affording procedural safeguards to a person arrested by the police. Whenever a person dies in custody of the police, Section 176 requires the Magistrate to hold and enquiry into the cause of death.
However, inspite of the constitutional and statutory provisions aimed at safeguarding the personal liberty and life of a citizen, growing incidence of torture and deaths in police custody has been a disturbing factor. Experience shows that worst violations of human rights take place during the course of investigation, when the police with a view to secure evidence or confession often resorts to third degree methods including torture and adopts techniques of screening arrest by either not recording the arrest or describing the deprivation of liberty merely as a prolonged interrogation. A reading of the morning newspapers almost everyday carrying reports of dehumanising torture, assault, rape and death in custody of police or other governmental agencies is indeed depressing. The increasing incidence of torture and death in custody has assumed such alarming proportions that it is affecting the creditibility of the Rule of Law and the administration of criminal justice system. The community rightly feels perturbed. Society’s cry for justice becomes louder.
The Third Report of the National Police Commission in India expressed its deep concern with custodial demoralising effect with custodial torture was creating on the society as a whole. It made some very useful suggestions. It suggested :
“……An arrest during the investigation of a cognizable case may be considered justified in one or other of the following circumstances :
(1) The case involves a grave offence like murder, dacoity, robbery, rape etc., and it is necessary to arrest the accused and bring his movements under restraint to infuse confidence among the terror stricken victims.
(ii) The accused is likely to abscond and evade the processes of law.
(iii) The accused is given to violent behaviour and is likely to commit further offences unless his movements are brought under restraint.
(iv) The accused is a habitual offender and unless kept in custody he is likely to commit similar offences again. It would be desirable to insist through departmental instructions that a police officer making an arrest should also record in the case diary the reasons for making the arrest, thereby clarifying his conformity to the specified guidelines….”
The recommendations of the Police Commission (supra) reflect the constitutional concomitants of the fundamental right to personal liberty and freedom. These recommendations, however, have not acquired any statutory status so far.
This Court in Joginder Kumar Vs. State (1994 (4) SCC, 260] (to which one of us, namely, Anand, J. was a party) considered the dynamics of misuse of police power of arrest and opined :
“No arrest can be made because it is lawful for the police officer to do so. The existence of the power of arrest is one thing. The justification for the exercise of it is quite another…No. arrest should be made without a reasonable satisfaction reached after some investigation about the genuineness and bonafides of a complaint and a reasonable belief both as to the person’s complicity and even so as to the need to effect arrest. Denying person his liberty is a serious matter.”
Joginder Kumar’s case (supra) involved arrest of a practising lawyer who had bee called to the police station in connection with a case under inquiry on 7.1.94. On not receiving any satisfactory account of his whereabouts, the family member of the detained lawyer preferred a petition in the nature of habeas corpus before this Court on 11.1.94 and in compliance with the notice, the lawyer was produced on 14.1.94 before this court the police version was that during 7.1.94 and 14.1.94 the lawyer was not in detention at all but was only assisting the police to detect some cases. The detenue asserted otherwise. This Court was not satisfied with the police version. It was noticed that though as on that day the relief in habeas corpus petition could not be granted but the questions whether there had been any need to detain the lawyer for 5 days and if at all he was not in detention then why was this Court not informed. Were important questions which required an answer. Besides, if there was detention for 5 days, for what reason was he detained. The Court’ therefore, directed the District Judge, Ghaziabad to make a detailed enquiry and submit his report within 4 weeks. The Court voiced its concern regarding complaints of violations of human rights during and after arrest. It said:
“The horizon of human rights is expanding, at the same time, the crime rate is also increasing, of late, this Court has been receiving complaints about violations of human rights because of indiscriminate arrests. How are we to strike a balance between the two?
……….. A realistic approach should be made in this direction. The law of arrest is one of balancing individual rights, liberties and privileges, on the one hand, and individual duties, obligations weighing and balancing the rights, liberties and privileges of he single individual and those of individuals collectively; of simply deciding what is wanted and where to put the weight and the emphasis; of deciding with comes first-the criminal or society, the law violator or the abider…..”
This Court then set down certain procedural “requirements” in cases of arrest.
Custodial death is perhaps one of the worst crimes in a civilised society governed by the Rule of Law. The rights inherent in Articles 21 and 22(1) of the Constitution required to be jealously and scrupulously protected. We cannot wish away the problem. Any form of torture of cruel, inhuman or degrading treatment would fall within the inhibition of Article 21 of the Constitution, whether it occurs during investigation, interrogation or otherwise. If the functionaries of the Government become law breakers, it is bound to breed contempt for law and would encourage lawlessness and every man would have the tendency to become law unto himself thereby leading to anarchanism. No civilised nation can permit that to happen. Does a citizen shed off his fundamental right to life, the moment a policeman arrests him? Can the right to life of a citizen be put in abeyance on his arrest? These questions touch the spinal court of human rights jurisprudence. The answer, indeed, has to be an emphatic ‘No’. The precious right guaranteed by Article 21 of the Constitution of India cannot be denied to convicted undertrials, detenues and other prisoners in custody, except according to the procedure established by law by placing such reasonable restrictions as are permitted by law.
In Neelabati Bahera Vs. State of Orissa (1993 (2) SCC, 746], (to which Anand, J. was a party) this Court pointed out that prisoners and detenues are not denuded of their fundamental rights under Article 21 and it is only such restrictions as are permitted by law, which can be imposed on the enjoyment of the fundamental rights of the arrestees and detenues. It was observed :
“It is axiomatic that convicts, prisoners or undertrials are not denuded of their fundamental rights under Article 21 and its is only such restrictions, as are permitted by law, which can be imposed on the enjoyment of the fundamental right by such persons. It is an obligation of the State to ensure that there is no infringement of the indefeasible rights of a citizen o life, except in accordance with law, while the citizen is in its custody. The precious right guaranteed by Article 21 of the constitution of India cannot be denied to convicts, undertrials or other prisoners in custody, expect according to procedure established by law. There is a great responsibility on the police or prison authorities to ensure that the citizen in its custody is not deprived of his right to life. His liberty is in the very nature of things circumscribed by the very fact of his confinement and therefore his interest in the limited liberty left to him is rather precious. The duty of care on the part of the State is responsible if the person in custody of the police is deprived of his life except according to the procedure established by law.
Instances have come to out notice were the police has arrested a person without warrant in connection with the investigation of an offence, without recording the arrest, and the arrest person has been subjected to torture to extract information from him for the purpose of further investigation or for recovery of case property or for extracting confession etc. The torture and injury caused on the body of the arrestee has sometime resulted into his death. Death in custody is not generally shown in the records of the lock-up and every effort is made by the police to dispose of the body or to make out a case that the arrested person died after he was released from custody. Any complaint against such torture or death is generally not given any attention by the police officers because of ties of brotherhood. No first information report at the instance of the victim or his kith and kin is generally entertained and even the higher police officers turn a blind eye to such complaints. Even where a formal prosecution is launched by the victim or his kith and kin, no direct evidence is available to substantiate the charge of torture or causing hurt resulting into death as the police lock-up where generally torture or injury is caused is away from the public gaze and the witnesses are either police men or co- prisoners who are highly reluctant to appear as prosecution witness due to fear of letaliation by the superior officers of the police. It is often seen that when a complaint is made against torture, death or injury, in police custody, it is difficult to secure evidence against the policemen responsible for resorting to third degree methods since they are incharge of police station records which they do not find difficult to manipulate. Consequently, prosecution against the delinquent officers generally results in acquittal. State of Madhya Pradesh Vs. Shyamsunder Trivedi & Ors. ( 1995 (3) Scale, 343 =] is an apt case illustrative of the observations made by us above. In that case, Nathu Bnjara was tortured at police station, Rampura during the interrogation. As a result of extensive injuries caused to him he died in police custody at the police station. The defence set up by the respondent police officials at the trial was that Nathu Banjara had been released from police custody at about 10.30 p.m. after interrogation 13.10.1986 itself vide entry EX, P/22A in the Roznamcha and that at about 7,00 a.m. on 14.10.1981, a death report Ex. P/9 was recorded at the police station, Rampura, at the instance of Ramesh respondent No. 6, to the effect that he had found “one unknown person” near a tree by the side of the tank riggling with pain in his chest and that as a soon as respondent No. 6 reached near him, the said person died. The further case set up by SI Trivedi, respondent No. 1, incharge of the police station was that after making a Roznamcha entry at 7.00 a.m. about his departure from the police station he (respondent No. 1 Shyamsunder Trivedi) and Constable Rajaram respondent proceeded to the spot where the dead body was stated to be lying for conducting investigation under Section 174 Cr.P.C. He summoned Ramesh Chandra and Goverdhan respondents to the spot and in their presence prepared a panchnama EX. P/27 of the dead body recording the opinion therein to the effect that no definite cause of death was known.
The First Additional Sessions Judge acquitted all the respondents of all the charges holding that there was no direct evidence to connect the respondents with the crime. The State of Madhya Pradesh went up in appeal against the order of acquittal and the High Court maintained the acquittal of respondents 2 to 7 but set aside the acquittal of respondent No. 1, Shyamsunder Trivedi for offences under Section 218, 201 and 342 IPC. His acquittal for the offences under Section 302/149 and 147 IPC was, however, maintained. The State filed an appeal in this court by special leave. This Court found that the following circumstances have been established by the prosecution beyond every reasonable doubt and coupled with the direct evidence of PWS 1, 3, 4, 8 and 18 those circumstances were consistent only with the hypothesis of the quilt of the respondents and were inconsistent with their innocence :
(a) that the deceased had been brought alive to the police station ad was last seen alive there on 13.10.81;
(b) That the dead body of the deceased was taken out of the police station on 14.1.81 at about 2 p.m. for being removed to the hospital;
(c) that SI Trivedi respondent No. 1, Ram Naresh shukla, Respondent and Ganiuddin respondent No. 5 were present at the police station and had all joined hands to dispose of the dead body of Nathu-Banjara:
(d) That si Trivedi, respondent No. 1 created false evidence and fabricated false clues in the shape of documentary evidence with a view to screen the offence and for that matter, the offender:
(e) SI Trivedi respondent in connivance with some of his subordinates, respondents herein had taken steps to cremate the dead body in haste describing the deceased as a ‘lavaris’ though the identity of the deceased, when they had interrogated for a sufficient long time was well known to them, and opined that:
“The observations of the High Court that the presence and participation of these respondents in the crime is doubtful are not borne out from the evidence on the record and appear to be an unrealistic over simplification of the tell tale circumstances established by the prosecution.”
One of us (namely, Anand, J.) speaking for the Court went on to observe :
“The trial court and the High Court, if we may say so with respect, exhibited a total lack of sensitivity and a ‘could not careless’ attitude in appreciating the evidence on the record and thereby condoning the barbarous there degree methods which are still being used, at some police stations, despite being illegal. The exaggerated adherence to and insistence upon the establishment of proof beyond every reasonable doubt, by the prosecution, ignoring the ground realities, the fact situations and the peculiar circumstances of a given case, as in the present case, often results in miscarriage of justice and makes the justice delivery system a suspect. In the ultimate analysis the society suffers and a criminal gets encouraged. Tortures in police custody, which of late are on the increase, receive encouragement by this type of an unrealistic approach of the Courts because it reinforces the belief in the mind of the police that no harm would come to them if an odd prisoner dies in the lock-up, because there would hardly be and evidence available to the prosecution to directly implicate them with the torture. The Courts, must not loose sight of the fact that death in police custody is perhaps on of the worst kind of crime in a a civilised society, governed by the rule of law and poses a serious thereat to an orderly civilised society.”
This Court then suggested : “The Courts are also required to have a change in their outlook and attitude, particularly in cases involving custodial crimes and they should exhibit more sensitivity and adopt a realistic rather than a narrow technical approach, while dealing with the case of custodial crime so that as far as possible within their powers, the guilty should not escape so that the victim of crime has the satisfaction that ultimately the Majesty of Law has prevailed.”
The State appeal was allowed and the acquittal of respondents 1, 3, 4 and 5 was set aside. The respondents were convicted for various offences including the offence under Section 304 Part 11/34 IPC and sentenced to various terms of imprisonment and fine ranging from Rs. 20,000/- to Rs.. 50,000/-. The fine was directed to be paid to the heirs of Nathu Banjara by way of compensation. It was further directed :
“The Trial Court shall ensure, in case the fine is deposited by the accused respondents, that the payment of the same is made to the heirs of deceased Nathu Banjara, and the Court shall take all such precautions as are necessary to see that the money is not allowed to fall into wrong hands and is utilised for the benefit of the members of the family of the deceased Nathu Banjara, and if found practical by deposit in nationalised Bank or post office on such terms as the Trial Court may in consultation with the heirs for the deceased consider fit and proper.”
It needs no emphasis to say that when the crime goes unpunished, the criminals are encouraged and the society suffers. The victim of crime or his kith and kin become frustrated and contempt for law develops. It was considering these aspects that the Law Commission in its 113th Report recommended the insertion of Section 114B in the Indian Evidence Act. The Law Commission recommended in its 113th Report that in prosecution of a police officer for an alleged offence of having caused bodily injury to a person, if there was evidence that the injury was caused during the period when the person was in the custody of the police, the Court may presume that the injury was caused by the police officer having the custody of the person during that period. The Commission further recommended that the court, while considering the question of presumption, should have regard to all relevant circumstances including the period of custody statement made by the victim, medical evidence and the evidence with the Magistrate may have recorded. Change of burden of proof was, thus, advocated. In sham Sunder Trivedi’s case (supra) this Court also expressed the hope that the Government and the legislature would give serious thought to the recommendation of the Law Commission, Unfortunately, the suggested amendment, has not been incorporated in the statute so far. The need of amendment requires no emphasis– sharp rise i custodial violence, torture and death in custody, justifies the urgency for the amendment and we invite Parliament’s attention to it.
Police is, no doubt, under a legal duty and has legitimate right to arrest a criminal and to interrogate him during the investigation of a an offence but it must be remembered that the law does not permit use of third degree methods or torture of accused in custody during interrogation and investigation with that view to solve the crime. End cannot justify the means. The interrogation and investigation into a crime should be in true sense purpose full to make the investigation effective. By torturing a person and using their degree methods, the police would be accomplishing behind the closed doors what the demands of our legal order forbid. No. society can permit it.
How do we check the abuse of police power? Transparency of action and accountability perhaps are tow possible safeguards which this Court must insist upon. Attention is also required to be paid to properly develop work culture, training and orientation of police force consistent with basic human values. Training methodology of the police needs restructuring. The force needs to be infused with basic human values and made sensitive to the constitutional ethos. Efforts must be made to change the attitude and approach of the police personal handling investigations so that they do not sacrifice basic human values during interrogation and do not resort to questionable form of interrogation. With a view to bring in transparency, the presence of the counsel of the arrestee at some point of time during the interrogation may deter the police from using third degree methods during interrogation.
Apart from the police, there are several other governmental authorities also like Directorate of Revenue Intelligence, Directorate of Enforcement, Costal Guard, Central Reserve Police Force (CRPF), Border Security Force (BSF), the Central Industrial Security Force (CISF), the State Armed Police, Intelligence Agencies like the Intelligence Bureau, R.A.W, Central Bureau of Investigation (CBI), CID, Tariff Police, Mounted Police and ITBP which have the power to detain a person and to interrogated him in connection with the investigation of economic offences, offences under the Essential Commodities Act, Excise and Customs Act. Foreign Exchange Regulation Act etc. There are instances of torture and death in custody of these authorities as well, In re Death of Sawinder Singh Grover (1995 Supp (4) SCC, 450], (to which Kuldip Singh, j. was a party) this Court took suo moto notice of the death of Sawinder Singh Grover during his custody with the Directorate of Enforcement. After getting an enquiry conducted by the additional District Judge, which disclosed a prima facie case for investigation and prosecution, this Court directed the CBI to lodge a FIR and initiate criminal proceeding against all persons named in the report of the Additional District Judge and proceed against them. The Union of India/Directorate of Enforcement was also directed to pay sum of Rs. 2 lacs to the widow of the deceased by was of the relevant provisions of law to protect the interest of arrested persons in such cases too is a genuine need.
There is one other aspect also which needs out consideration, We are conscious of the fact that the police in India have to perform a difficult and delicate task, particularly in view of the deteriorating law and order situation, communal riots, political turmoil, student unrest, terrorist activities, and among others the increasing number of underworld and armed gangs and criminals, Many hard core criminals like extremist, the terrorists, drug peddlers, smugglers who have organised gangs, have taken strong roots in the society. It is being said in certain quarters that with more and more liberalisation and enforcement of fundamental rights, it would lead to difficulties in the detection of crimes committed by such categories of hardened criminals by soft peddling interrogation. It is felt in those quarters that if we lay to much of emphasis on protection of their fundamental rights and human rights such criminals may go scot-free without exposing any element or iota or criminality with the result, the crime would go unpunished and in the ultimate analysis the society would suffer. The concern is genuine and the problem is real. To deal with such a situation, a balanced approach is needed to meet the ends of justice. This all the more so, in view of the expectation of the society that police must deal with the criminals in an efficient and effective manner and bring to book those who are involved in the crime. The cure cannot, however, be worst than the disease itself.
The response of the American supreme Court to such an issue in Miranda Vs. Arizona, 384 US 436 is instructive. The Court said :
“A recurrent argument, made in these cases is that society’s need for interrogation out-weighs the privilege. This argument is not unfamiliar to this Court. See. e.g. Chambers v. Florida, 309 US 227, 240-41, 84 L ed 716, 724, 60 S Ct 472 (1940). The whose thrust of out foregoing discussion demonstrates that the Constitution has prescribed the rights of the individual when confronted with the power of Government when it provided in the Fifth Amendment that an individual cannot be compelled to be a witness against himself. That right cannot be abridged.”
(Emphasis ours) There can be no gain saying that freedom of an individual must yield to the security of the State. The right of preventive detention of individuals in the interest of security of the State in various situations prescribed under different statures has been upheld by the Courts. The right to interrogate the detenues, culprits or arrestees in the interest of the nation, must take precedence over an individual’s right to personal liberty. The latin maxim salus populi est supreme lex (the safety of the people is the supreme law) and salus republicae est suprema lex (safety of the state is the supreme law) co-exist an dare not only important and relevant but lie at the heart of the doctrine that the welfare of an individual must yield to that of the community. The action of the State, however must be “right, just and fair”. Using any form of torture for extracting any kind of information would neither be “right nor just nor fair’ and, therefore, would be impermissible, being offensive to Article 21. Such a crime suspect must be interrogated– indeed subjected to sustained and scientific interrogation determined in accordance with the provisions of law. He cannot, however, be tortured or subjected to third degree methods or eleminated with a view to elicit information, extract confession or drive knowledge about his accomplices, weapons etc. His Constitutional right cannot be abridged except in the manner permitted by law, though in the very nature of things there would be qualitative difference in the methods of interrogation of such a person as compared to an ordinary criminal. Challenge of terrorism must be met wit innovative ideas and approach. State terrorism is not answer to combat terrorism. State terrorism is no answer to combat terrorism. State terrorism would only provide legitimacy to ‘terrorism’. That would be bad for the State, the community and above all for the Rule of Law. The State must, therefore, ensure that various agencies deployed by it for combating terrorism act within the bounds of law and not become law unto themselves, that the terrorist has violated human rights of innocent citizens may render him liable for punishment but it cannot justify the violation of this human rights expect in the manner permitted by law. Need, therefore, is to develop scientific methods of investigation and train the investigators properly to interrogate to meet the challenge.
In addition to the statutory and constitutional requirements to which we have made a reference, we are of the view that it would be useful and effective to structure appropriate machinery for contemporaneous recording and notification of all cases of arrest and detention to bring in transparency and accountability. It is desirable that the officer arresting a person should prepare a memo of his arrest on witness who may be a member of the family of the arrestee or a respectable person of the locality from where the arrest is made. The date and time of arrest shall be recorded in The memo which must also be counter signed by the arrestee.
We therefore, consider it appropriate to issue the following requirements to be followed in all cases of arrest or detention till legal provisions are made in that behalf as preventive measures :
(1) The police personnel carrying out the arrest and handling the interrogation of the arrestee should bear accurate, visible and clear identification and name togs with their designations. The particulars of all such police personnel who handle interrogation of the arrestee must be recorded in a register.
(2) That the police officer carrying out the arrest of the arrestee shall prepare a memo of arrest at the time of arrest a such memo shall be attested by atleast one witness. who may be either a member of the family of the arrestee or a respectable person of the locality from where the arrest is made. It shall also be counter signed by the arrestee and shall contain the time and date of arrest.
(3) A person who has been arrested or detained and is being held in custody in a police station or interrogation centre or other lock-up, shall be entitled to have one friend or relative or other person known to him or having interest in his welfare being informed, as soon as practicable, that he has been arrested and is being detained at the particular place, unless the attesting witness of the memo of arrest is himself such a friend or a relative of the arrestee.
(4) The time, place of arrest and venue of custody of an arrestee must be notified by the police where the next friend or relative of the arrestee lives outside the district or town through the legal Aid Organisation in the District and the police station of the area concerned telegraphically within a period of 8 to 12 hours after the arrest.
(5) The person arrested must be made aware of this right to have someone informed of his arrest or detention as soon he is put under arrest or is detained.
(6) An entry must be made in the diary at the place of detention regarding the arrest of the person which shall also disclose the name of he next friend of the person who has been informed of the arrest an the names and particulars of the police officials in whose custody the arrestee is.
(7) The arrestee should, where he so requests, be also examined at the time of his arrest and major and minor injuries, if any present on his/her body, must be recorded at that time. The “Inspection Memo” must be signed both by the arrestee and the police officer effecting the arrest and its copy provided to the arrestee.
(8) The arrestee should be subjected to medical examination by trained doctor every 48 hours during his detention in custody by a doctor on the panel of approved doctors appointed by Director, Health Services of the concerned Stare or Union Territory. Director, Health Services should prepare such a penal for all Tehsils and Districts as well.
(9) Copies of all the documents including the memo of arrest, referred to above, should be sent to the illaga Magistrate for his record.
(10) The arrestee may be permitted to meet his lawyer during interrogation, though not throughout the interrogation.
(11) A police control room should be provided at all district and state headquarters, where information regarding the arrest and the place of custody of the arrestee shall be communicated by the officer causing the arrest, within 12 hours of effecting the arrest and at the police control room it should be displayed on a conspicuous notice board.
Failure to comply with the requirements hereinabove mentioned shall apart from rendering the concerned official liable for departmental action, also render his liable to be punished for contempt of court and the proceedings for contempt of court may be instituted in any High Court of the country, having territorial jurisdiction over the matter.
The requirements, referred to above flow from Articles 21 and 22 (1) of the Constitution and need to be strictly followed. These would apply with equal force to the other governmental agencies also to which a reference has been made earlier.
These requirements are in addition to the constitutional and statutory safeguards and do not detract from various other directions given by the courts from time to time in connection with the safeguarding of the rights and dignity of the arrestee.
The requirements mentioned above shall be forwarded to the Director General of Police and the Home Secretary of every Stare/Union Territory and it shall be their obligation to circulate the same to every police station under their charge and get the same notified at every police station at conspicuous place. It would also be useful and serve larger interest to broadcast the requirements on the All India Radio besides being shown on the National network of Doordarshan and by publishing and distributing pamphlets in the local language containing these requirements for information of the general public. Creating awareness about the rights of the arrestee would in out opinion be a step in the right direction to combat the evil of custodial crime and bring in transparency and accountability. It is hoped that these requirements would help to curb, if not totally eliminate, the use of questionable methods during interrogation and investigation leading to custodial commission of crimes.
PUNITIVE MEASURES UBI JUS IBI REMEDIUM– There is no wrong without a remedy. The law will that in every case where man is wronged and undamaged he must have a remedy. A mere declaration of invalidity of an action or finding of custodial violence or death in lock-up does not by itself provide any meaningful remedy to a person whose fundamental right to life has been infringed. Much more needs to be done.
Some punitive provisions are contained in the Indian Penal Code which seek to punish violation of right to life. Section 220 provides for punishment to an officer or authority who detains or keeps a person in confinement with a corrupt or malicious motive. Section 330 and 331 provide for punishment of those who inflict injury of grievous hurt on a person to extort confession or information in regard to commission of an offence. Illustration (a) and (b) to Section 330 make a police officer guilty of torturing a person in order to induce him to confess the commission of a crime or to induce him to confess the commission of a crime or to induce him to point out places where stolen property is deposited. Section 330, therefore, directly makes torture during interrogation and investigation punishable under the Indian Penal Code. These Statutory provisions are, However, inadequate to repair the wrong done to the citizen. Prosecution of the offender is an obligation of the State in case of every crime but the victim of crime needs to be compensated monetarily also. The Court, where the infringement of the fundamental right is established, therefore, cannot stop by giving a mere declaration. It must proceed further and give compensatory relief, nor by way of damages as in a civil action but by way of compensation under the public law jurisdiction for the wrong done, due to breach of public duty by the State of not protecting the fundamental right to life of the citizen. To repair the wrong done and give judicial redress for legal injury is a compulsion of judicial conscience.
Article 9(5) of the International convent on civil and Political Rights, 1966 (ICCPR) provides that “anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have enforceable right to compensation”, of course, the Government of India as the time of its ratification (of ICCPR) in 1979 had made a specific reservation to the effect that the Indian legal system does not recognise a right to compensation for victims of unlawful arrest or detention and thus did not become party to the Convent. That reservation, however, has now lost its relevance in view of the law laid down by this Court in number of cases awarding compensation for the infringement of the fundamental right to life of a citizen. (See with advantage Rudal Shah Vs. State of Bihar ( 1983 (4) SCC, 141 ]: Sebastian M. Hongrey Vs. Union of India ( 1984 (3) SCC, 339] and 1984 (3) SCC, 82]; Bhim Singh Vs State of J & K (1984 (Supp) SCC, 504 and 1985 (4) SCC, 677] Saheli Vs. Commissioner of Police. Delhi [1990 (1) SCC 422]). There is indeed no express provision in the Constitution of India for grant of compensation for violation of a fundamental right to life, nonetheless, this Court has judicially evolved a right o compensation in cases of established unconstitutional deprivation of person liberty or life. (See : Nilabati Bahara Vs. State (Supra)] till about tow decades ago the liability of the government for tortious act of its public servants as generally limited and the person affected could enforce his right in tort by filing a civil suit and there again the defence of sovereign immunity was allowed to have its play. For the violation of the fundamental right to life or the basic human rights, however, this Court has taken the view that the defence of sovereign immunity is not available to the State for the tortious act of the public servants and for the established violation of the rights guaranteed by Article 21 of the Constitution of India. In Nilabati Behera Vs. State (supra) the decision of this Court in Kasturi Lal Ralia Ram Jain Vs. State of U.P. [1965 (1) SCR, 375] wherein the plea of sovereign immunity had been upheld in a case of vicarious liability of the State for the tort committed by its employees was explained thus:
“In this context, it is sufficient to say that the decision of this Court in Kasturilal upholding the State’s plea of sovereign immunity for tortious acts of its servants is confined to the sphere of liability in tort, which is distinct from the State’s liability for contravention of fundamental rights to which the doctrine of sovereign immunity has no application in the constitutional remedy under Articles 32 and 226 of the Constitution which enables award of compensation for contravention of fundamental rights, when the only practicable mode of enforcement of the fundamental rights can be the award of compensation. The decisions of this court in Rudul Sah and others in that line relate to award of compensation for contravention of fundamental rights, in the constitutional remedy upon Articles 32 and 226 of the Constitution, On the other hand, Kasturilal related to the value of goods seized and not returned to the owner due to the fault of government Servants, the claim being of damages of the tort of conversion under the ordinary process, and not a claim for compensation for violation of fundamental rights. Kasturilal is, therefore, inapplicable in this context and distinguishable.”
The claim in public law for compensation for unconstitutional deprivation of fundamental right to life and liberty, the protection of which is guaranteed under the Constitution, is a claim based on strict liability and is in addition to the claim available in private law for damages of tortious acts of the public servants. Public law proceedings serve a different purpose than the private law proceedings. Award of compensation for established infringement of the indefeasible rights guaranteed under Article 21 of the Constitutions is remedy available in public law since the purpose of public law is not only to civilise public power but also to assure the citizens that they live under a legal system wherein their rights and interests shall be protected and preserved. Grant of compensation in proceedings under Article 32 or 226 of the Constitution of India for the established violation or the fundamental rights guaranteed under Article 21, is an exercise of the Courts under the public law jurisdiction for penalising the wrong door and fixing the liability for the public wrong on the State which failed in the discharge of its public duty to protect the fundamental rights of the citizen.
The old doctrine of only relegating the aggrieved to the remedies available in civil law limits the role of the courts too much, as the protector and custodian of the indefeasible rights of the citizens. The courts have the obligation to satisfy the social aspirations of the citizens because the court and the law are for the people and expected to respond to their aspirations. A Court of law cannot close its consciousness and aliveness to stark realities. Mere punishment of the offender cannot give much solace to the family of the victim– civil action for damage is a long drawn and cumber some judicial process. Monetary compensation for redressal by the Court finding the infringement of the indefeasible right to life of the citizen is, therefore, useful and at times perhaps the only effective remedy to apply balm to the wounds of the family members of the deceased victim. Who may have been the bread winner of the family.
In Nilabati Bahera’s case (supra), it was held: “Adverting to the grant of relief to the heirs of a victim of custodial death for the infraction or invasion of his rights guaranteed under Article 21 of the Constitution of India, it is not always enough to relegate him to the ordinary remedy of a civil suit to claim damages for the tortious act of the State as that remedy in private law indeed is available to the aggrieved party. The citizen complaining of the infringement of the indefeasible right under Article 21 of the constitution cannot be told that for the established violation of the fundamental right to life he cannot get any relief under the public law by the courts exercising Writ jurisdiction, The primary source of the public law proceedings stems from the prerogative writs and the courts have therefore, to evolve’ new tools’ to give relief in public law by moulding it according to the situation with a view to preserve and protect the Rule of Law. While concluding his first Hamlyn Lecture in 1949 under the title “freedom under the Law” Lord Denning in his own style warned :
No one ca suppose that the executive will never be guilty the of the sins that are common to all of us. Your may be sure that they will sometimes to things which they ought to do : and will not do things that they ought to do. But if and when wrongs are thereby suffered by any of us what is the remedy? Our procedure for securing our personal freedom is efficient, out procedure for preventing the abuse of power is not. Just as the pick and shovel is no longer suitable for the winning of coal, so also the procedure of mandamus, certiorari and actions on the case are not suitable for the winning or freedom in the new age. They must be replaced by new and up-to date machinery by declarations, injunctions and actions for negligence… This is not the task of Parliament… the courts must do this. Of all the great tasks that lie ahead this is the greatest.
Properly exercised the new powers of the executive lead to the welfare state : but abused they lead to a totalitarian state. None such must ever be allowed in this country.”
A similar approach of redressing the wrong by award of monetary compensation against the State for its failure to protect the fundamental rights of the citizen has been adopted by the Courts of Ireland, which has a written constitution, guaranteeing fundamental rights, but which also like the Indian Constitution contains no provision of remedy for the infringement of those rights. That has, however, not prevented the Court in Ireland from developing remedies, including the award of damages, not only against individuals guilty of infringement, but against the State itself.
The informative and educative observations of O’ Dalaigh CJ in The State (At the Prosecution of Quinn) v. Ryan [1965] IR 70 (122) deserve special notice. The Learned Chief Justice said:
“It was not the intention of the Constitution in guaranteeing the fundamental rights of the citizen that these rights should be set at nought or circumvented. The intention was that rights of substances were being assured to the individual and that the Courts were the custodians of those rights. As a necessary corollary, it follows that no one can with impunity set these rights at nought of circumvent them, and that the Court’s powers in this regard are as ample as the defence of the Constitution require.”
(Emphasis supplied) In Byrne v. Ireland (1972) IR 241, Walsh J opined at p 264:
“In several parts in the Constitution duties to make certain provisions for the benefit of the citizens are imposed on the State in terms which bestow rights upon the citizens and, unless some contrary provision appears in the Constitution, the Constitution must be deemed toe have created a remedy for the enforcement of these rights. It follows that, where the right is one guaranteed by the State. It is against the State that the remedy must be sought it there has been a failure to discharge the constitutional obligation impose”
(Emphasis supplied) In Maharaj Vs. Attorney General of Trinidad and Tobago ( (1978) 2 All E.R. 670). The Privy Council while interpreting Section 6 of the Constitution of Trinidad and Tobago held that though not expressly provided therein, it permitted an order for monetary compensation, by way of ‘redress’ for contravention of the basic human rights and fundamental freedoms. Lord Diplock speaking for the majority said:
“It was argued on behalf of the Attorney General that Section 6(2) does not permit of an order for monetary compensation despite the fact that this kind of redress was ordered in Jaundoo v. Attorney General of Guyana. Reliance was placed on the reference in the sub- section to ‘enforcing, or securing the enforcement of any of the provisions of the said foregoing sections’ as the purpose for which orders etc. could be made. An order for payment of compensation, it was submitted, did not amount to the enforcement of the rights that had been contravened. In their Lordships’ view of order for payment of compensation when a right protected under Section 1 ‘has been contravened is clearly a form of ‘redress’ which a person is entitled to claim under Section 6 (1) and may well be any only practicable form of redress, as by now it is in the instant case. The jurisdiction to make such an order is conferred on the High Court by para (a) of Section 6(2), viz. jurisdiction ‘to here and determine any application made by any person in pursuance of sub-section (1) of this section’. The very wide power to make orders, issue writs and give directions are ancillary to this.”
Lord diplock then went on to observe ( at page 680) : “Finally, their Lordships would say something about the measure of monetary compensation recoverable under Section 6 where the contravention of the claimant’s constitutional rights consists of deprivation of liberty otherwise that by due process of law. The claim is not a claim in private law for damages for the tort of false imprisonment, under which the damages recoverable are at large and would include damages for loss of reputation. It is a claim in public law for compensation for deprivation of liberty alone.”
In Simpson was, Attorney General [ Baigent’s case ] (1994 NZLR, 667) the Court of Appeal in New Zealand dealt with the issue in a very elaborate manner by reference to a catena of authorities from different jurisdictions. It considered the applicability of the doctrine of vicarious liability for torts, like unlawful search, committed by the police officials which violate the New Zealand Bill of Rights Act, 1990. While dealing with the enforcement of rights and freedoms as guaranteed by the Bill of Rights for which no specific remedy was provided. Hardie Boys, J. observed :
“The New Zealand Bill of Rights Act, unless it is to be no more that an empty statement, is a commitment by the Crown that those who in the three branches of the government exercise its functions, powers and duties will observe the rights hat the Bill affirms. it is I consider implicit in that commitment, indeed essential to its worth, that the Courts are not only to observe the Bill in the discharge of their own duties but are able to grant appropriate ad effective remedies where rights have been infringed. I see no reason to think that this should depend on the terms of a written constitution. Enjoyment of the basic human rights are the entitlement of every citizen, and their protection the obligation of every civilised state. They are inherent in and essential to the structure of society. They do not depend on the legal or constitutional form in which they are declared. the reasoning that has led the Privy Council and the Courts of Ireland and India to the conclusions reached in the cases to which I have referred (and they are but a sample) is in my opinion equally valid to the New Zealand Bill of Rights Act if it is to have life and meaning.” (Emphasis supplied) The Court of appeal relied upon the judgment of the Irish Courts, the Privy Council and referred to the law laid down in Nilabati Behera Vs. State (supra) thus:
“Another valuable authority comes from India, where the constitution empowers the Supreme Court to enforce rights guaranteed under it. In Nilabati Bahera V. State of Orissa (1993) Cri. LJ 2899, the Supreme Court awarded damages against the Stare to the mother of a young man beaten to death in police custody. The Court held that its power of enforcement imposed a duty to “forge new tools”, of which compensation was an appropriate on where that was the only mode of redress available. This was not a remedy in tort, but one in public law based on strict liability for the contravention of fundamental rights to which the principle of sovereign immunity does not apply. These observations of Anand, J. at P 2912 may be noted.
The old doctrine of only relegating the aggrieved to the remedies available in civil law limits the role of the courts too much as protector and guarantor of the indefeasible rights of the citizens. The courts have the obligation to satisfy the social aspirations of the citizens because the courts and the law are for the people and expected to respond to their aspirations. The purpose of public law is not only to civilize public that they live under a legal system which aims to protect their interest and preserve their rights.”
Each the five members of the Court of Appeal in Simpson’s case (supra) delivered a separate judgment but there was unanimity of opinion regarding the grant of pecuniary compensation to the victim, for the contravention of his rights guaranteed under the Bill of Rights Act, notwithstanding the absence of an express provision in that behalf in the Bill of Rights Act.
Thus, to sum up, it is now a well accepted proposition in most of the jurisdictions, that monetary or pecuniary compensation is an appropriate and indeed an effective and sometimes perhaps the only suitable remedy for redressal of the established infringement of the fundamental right to life of a citizen by the public servants and the State is vicariously liable for their acts. The claim of the citizen is based on the principle of strict liability to which the defence of sovereign immunity is nor available and the citizen must revive the amount of compensation from the State, which shall have the right to be indemnified by the wrong doer. In the assessment of compensation, the emphasis has to be on the compensatory and not on punitive element. The objective is to apply balm to the wounds and not to punish the transgressor or the offender, as awarding appropriate punishment for the offender, as awarding appropriate punishment for the offence (irrespective of compensation) must be left to the criminal courts in which the offender is prosecuted, which the State, in law, is duty bound to do, That award of compensation in the public law jurisdiction is also without prejudice to any other action like civil suit for damages which is lawfully available to the victim or the heirs of the deceased victim with respect to the same matter for the tortious act committed by the functionaries of the State. The quantum of compensation will. of course, depend upon the peculiar facts of each case and no strait jacket formula can be evolved in that behalf. The relief to redress the wrong for the established invasion of the fundamental rights of the citizen, under he public law jurisdiction is, in addition to the traditional remedies and not it derrogation of them. The amount of compensation as awarded by the Court and paid by the State to redress The wrong done, may in a given case, be adjusted against any amount which may be awarded to the claimant by way of damages in a civil suit.
Before parting with this judgment we wish to place on record our appreciation for the learned counsel appearing for the States in general and Dr. A.M. Singhvi, learned senior counsel who assisted the Court amicus curiae in particular for the valuable assistances rendered by them. (Soures : http://indiankanoon.org/doc/501198/)
আদালত জাগ্রত! মানবাধিকার কমিশন জাগ্রত! তবুও পুলিশ পুলিশই আছে। পুলিশই বিচারক, পুলিশই দণ্ডদাতা, পুলিশই হত্যাকারী। সারা পৃথিবী জুড়ে কত যে হাজার হাজার নিরীহ অসহায় মানুষের মৃত্যু হয় শুধুমাত্র পুলিশের গুলিতে, তার হিসাব কে রাখছে!
পশ্চিমবঙ্গকে সরিয়ে রেখে ভারতের অন্য রাজ্যগুলির দিকে একটু তাকালে একই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি দেখতে পারবেন। ভারতের বাইরে অন্যান্য তথাকথিত সভ্য দেশগুলিতেও নির্বিচারে মানুষ হত্যা করা হয়। সেগুলি কিছু উল্লেখ করতে মন চাইছে। বীভৎসতার বিচারে কিছু বাছাই ঘটনা।
১. আতঙ্কিত করা, যথেচ্ছ প্রহার, যন্ত্রণা দেওয়া, ভয় দেখানো এবং শেষ পর্যায়ে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারায় গেস্টাপো (গেহেইম স্ট্যাটসপোলজে) ছিল সিদ্ধহস্ত। গেস্টাপো, জার্মানের একটি সিক্রেট পুলিশ সংস্থা। গেস্টাপো ছিল মানুষের তৈরি জঘন্য, নৃশংস, হিংস্র এক সংস্থা। জার্মানিতে একটা সময় এসেছিল যখন গেস্টাপোর নাম শুনলে সাধারণ মানুষ আতঙ্কে শিউরে উঠত। বন্ধ হয়ে যেত হৃদস্পন্দন। নিরপরাধ মানুষদের উপর অকথ্য অত্যাচার করত এই সংস্থা। “ফ্রিডম অফ মুভমেন্ট’ ও ‘ফ্রিডম অফ স্পিচ’ যদি কোনো জার্মান নাগরিক চাইত, তবে তাঁদের যৌনাঙ্গে ইলেকট্রোডের শক, মহিলাদের ধর্ষণ, গোড়ালিতে দড়ি বেঁধে ছাদ থেকে ঝুলিয়ে চিরতরে পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য গাঁইতির হাতল বা রবারের ডাণ্ডা বা বিষাক্ত ইঞ্জেকশন প্রয়োগ করা হত। অত্যাচারের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিরপরাধ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা হত।
২. রাশিয়ার পুলিশ সংস্থা কেজিবি। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অসামরিক গোয়েন্দা পুলিশ বাহিনী ‘কমিটেট গাসুদোস্তভেন্নই বেজোপোসনোস্তি’, সংক্ষেপে কেজিবি। নাম শুনলেই প্যান্টে হিস্যু হয়ে যাবে অসাড়ে। সরকার চালাত কমিউনিস্ট পার্টি, আর সেই সরকারের নির্দেশে কেজিবি সাধারণ মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার করত। ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, রাশিয়ার সিক্রেট পুলিশ বাহিনী কাজ করেছে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে। জারের আমলে রাজ্যপাট চালাতে অন্যান্য সরকারি দপ্তরের চেয়ে সিক্রেট পুলিশকে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হয়েছিল। এটা গড়ে ওঠার পর থেকে এই পুলিশ বাহিনী কত লক্ষ রুশ নাগরিককে যে হত্যা করেছে তার হিসাব নেই।
৩, ইরাকের সিক্রেট সিকিউরিটি পুলিশ। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সামরিক সরকারের সঙ্গে কুর্দদের সংঘর্ষ লেগেই থাকত। শিশু, মহিলা, পুরুষ নির্বিশেষে সুযোগ পেলেই নিরপরাধ কুর্দদের ঠান্ডা মাথায় খুন করত ইরাকের সিক্রেট পুলিশ। সাদ্দামের সামরিক সরকার প্রায় ৩০০০ সাধারণ নিরীহ কুর্দদের হত্যা করেছিল বলে জানা যায়।
৪. ওজিপিইউ, অর্থাৎ ইউনাইটেট স্টেট পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন’। এই পুলিশ সংস্থাটি রাশিয়ার আর-একটি ঘাতকের দল। সামরিক বাহিনীতে কারা প্রশাসন ও পার্টির সমালোচক, অন্য অর্থে বিপ্লবের প্রতিবন্ধক বা দেশের শত্রু, তাঁদের খুঁজে বের করার কাজে ওজিপিইউ প্রথমদিকে ব্যস্ত থাকলেও পরে রাশিয়ার বৃহত্তম গণহত্যার জন্য এই সংস্থাকে ব্যবহার করা হয়েছিল। তিরিশের দশকে যখন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের কালেকটিভাইজেশন প্রোগ্রাম’-এ রূপান্তরিত হয় তখন দেশের কৃষকরা এর বিরুদ্ধে সোচ্চারে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। ওই প্রতিবাদী কৃষকদের কণ্ঠস্বরকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিয়েছিল এই ওজিপিইউ। রাশিয়ার ইতিহাস অনুযায়ী বিশ্বযুদ্ধের সময় দুই কোটি রুশ নাগরিক জার্মানদের হাতে নিহত হয়েছিল। কিন্তু তার আগে তিরিশের দশকে প্রায় সমসংখ্যক রুশি কৃষককে সে দেশের সরকার গুলি করে, ফাঁসি দিয়ে, বেয়নেটে বিদ্ধ করে ও লেবার ক্যাম্পে পাঠিয়ে হত্যা করেছিল। এই গণহত্যার নায়ক পরবর্তীকালে তাঁর কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা পর্যন্ত করেননি, বরং আমজনতার সামনে তা গর্ব করে বলতেন। প্রথমদিকে অবশ্য ব্যাপারটা চেপে রাখার চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানরা যখন সব ফাঁস করে দেয়, তখনই এই নৃশংস কৃষক হত্যার কথা বিশ্ববাসী জানতে পেরেছিল। স্তালিনের দ্বিতীয় স্ত্রী নাজেদদা এই গণহত্যার মানসিক চাপ সহ্য করতে না-পেরে শেষপর্যন্ত আত্মহত্যা করেছিল।
৫. দেশের নাম আর্জেন্টিনা। তখন আর্জিন্টিনার রাষ্ট্রপ্রধান কর্নেল জুয়ান ডোমিঙ্গো পেরন। ‘ডিভিশন দ্য ইনফরমেশন পলিটিকাস অ্যান্টিডোমোক্রেটিকাস’ হল সিক্রেট পুলিশের দল। সংক্ষেপে ‘ডিপা। নিপীড়ন, নির্যাতন ও প্রচণ্ড অত্যাচারের জন্য অল্পদিনের মধ্যেই ‘ডিপা’ বিখ্যাত হয়ে ওঠে। আন্দোলন দমনের কাজে এই সিক্রেট পুলিশ বাহিনীকে সাহায্য করত ‘আলিজায়া অ্যান্টি কমিউনাস্টা আর্জেন্টিনা’ ও ‘কমান্ডো লিবারোটেডোরস দ্য আমেরিকান নামের দুটি দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক গুণ্ডার দল, যাঁদের প্রত্যক্ষ মদত দিতেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট পেরন। রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতার পর ভালো করে হাত-পা বেঁধে লরিতে তোলা হত। এরপর কবরখানায় নিয়ে গিয়ে আগে থেকে খোঁড়া ট্রেঞ্চের সামনে জোর করে বসানো হত তাঁদের। অবধারিত মৃত্যুর জন্য আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হত না হতভাগ্য বন্দিদের। অকস্মাৎ পিছন থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মেশিনগানের গুলি এসে ঝাঁঝরা করে দিত ওদের শরীর। রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহগুলি গড়িয়ে পড়ত ট্রেঞ্চের ভিতরে। অনেক সময় ভারপ্রাপ্ত অফিসার বন্দিদের মৃত্যুর আগে শেষবার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার জন্য পাঁচ মিনিট সুযোগ দিত। গুলি করার আগে বন্দিদের জানানো হত সরকারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাঁদের এই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে। যাই হোক, ট্রেঞ্চে মৃতদেহের স্তূপ জমে উঠলে তরল দাহ্য বস্তু ছড়িয়ে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হত। এই সিক্রেট পুলিশের কীর্তিকলাপের এখানেই শেষ নয়। পৈশাচিক আনন্দের জন্য এঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক শক দিত পুরুষ বন্দিদের অণ্ডকোশে। মহিলা বন্দিদের বৈদ্যুতিক শক দেওয়া হত স্তনবৃন্তে। বন্দিদের মাথার উপর কয়েক কুইন্টাল ওজনের ভেজা ভূষির বস্তা চাপিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অত্যাচার চালাতে চালাতে পুলিশ বা আর্মির লোকেরা ক্লান্ত হয়ে পড়লে বিশ্রামের সময় সিগারেট ধরাত। ওই সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরো নেভাতে মহিলাদের যৌনাঙ্গকে অ্যাসট্রে হিসাবে ব্যবহার করত। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের এক রিপোর্ট অনুযায়ী ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আর্জেন্টিনায় অন্তত ৫০০০ পরিচিত রাজনৈতিক কর্মী চিরতরে হারিয়ে গেছেন।
৬. দেশের নাম কলম্বিয়া। গোপন পুলিশ সংস্থার নাম ‘মুয়ের্তে এ সিকুয়েস্ট্রেটস’, সংক্ষেপে ‘মাস’। গ্রেফতার ও অপহরণের পর সাধারণ মানুষকে হত্যা করায় সিদ্ধহস্ত ছিল এই স্কোয়াড। ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দে ৩০০০ বন্দিকে বিনাবিচারে হত্যা করে এই ডেথ স্কোয়াড। কলম্বিয়ার ম্যাগডালেনা মিডিও এলাকায় ফাওয়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী হাজার খানেক দরিদ্র কৃষক পতিত জমি পরিষ্কার করে উন্নত পদ্ধতিতে চাষবাস শুরু করে। বছর দুই/তিন ভালো ফসল পেয়েছিল ওই কৃষকেরা। এটাই চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়াল। ভাড়াটে সেনা ও ডেথ স্কোয়াড মাস’ একসঙ্গে ৮০০ কৃষককে হত্যা করেছিল কোনোরকম প্ররোচনা ছাড়াই।
৭. উগান্ডা, আফ্রিকা মহাদেশের একটি রাষ্ট্র। ইদি আমিনের শাসনকাল। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ– ইদি আমিনের রাজত্বকালের এই ৯ বছরে উগান্ডায় কমপক্ষে ১ লক্ষ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। এই নিহতের আসল হিসাবে ১০ লক্ষও ছাপিয়ে যেতে পারে। প্রকৃত হিসাব কারোরই জানা নেই।
না, আর নয়। সারা পৃথিবী জুড়ে পুলিশ কর্তৃক ধৃতদের হত্যা করার এত ঘটনা পাওয়া যায় যে, চমকে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। হাড় হিম করা সেসব কীর্তি।
“…‘নৈরাজ্য’ শব্দটার ভিতরে আছে ‘রাজা’ বিষয়ক ধ্যানধারণা। আসলে রাজ, বিরাজ, রাজ্য, রাজা, রাজন, সম্রাট, রাষ্ট্র প্রভৃতি শব্দের আদিতে আছে ‘রাজ’ নামের ধাতুটি (হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বঙ্গীয় শব্দকোষ, পৃষ্ঠা ১৯০৭)। এই ‘রাজ’-এর অর্থ হচ্ছে ‘শোভা’, ‘দীপ্তি’ (হরিচরণ)। এই ধাতু থেকে উৎপত্তি লাভ করা রাজ’ শব্দটির অর্থ ‘শোভা পাওয়া’, ‘দীপ্তি পাওয়া’, ‘প্রকাশ পাওয়া’, ‘বিদ্যমান থাকা’। এইভাবে ‘বিরাজ’ শব্দের অর্থ ‘শোভমান’, ‘শোভিত’, ‘দীপ্যমান’, দীপ্ত’; কিংবা শোভা পাওয়া’, ‘শোভিত হওয়া’, ‘শোভা করে অবস্থান করা’, ‘বিদ্যমান থাকা’, ‘উপস্থিত থাকা’। সম্রাট’ শব্দেরও অন্যতম অর্থ ‘রাজা’, এর গোড়ায় আছে ‘সম্ + রাজ + কিপ’, অর্থাৎ ‘যিনি মণ্ডলেশ্বর ও রাজগণের শাসক, তিনি সম্রাট। তার মানে যিনি শোভা পান, যিনি দীপ্তি পান, যিনি প্রকাশ পান, যিনি বিদ্যমান থাকেন, তিনিই হন রাজা।
কিন্তু ‘রাজা’ ছাড়া বাকি সব মানুষ কি শোভা পান না? দীপ্তি পান না? প্রকাশ পান না? বিদ্যমান থাকেন না? নিশ্চয়ই পান, নিশ্চয়ই থাকেন। কিন্তু রাজা’ ছাড়া অন্যসব লোকের শোভা, দীপ্তি, প্রকাশ, বিদ্যমানতা প্রভৃতির বিশেষ কোনো মূল্য ‘আইনত’ নেই (আইন এখানে রাজার আইন, রাষ্ট্রের আইন)। কেননা ‘রাজা’ ছাড়া অন্যসব ব্যক্তি যদিও শোভা পান, দীপ্তি পান, প্রকাশিত হন, বিদ্যমান থাকেন, তাহলে আর ‘রাজা’-র সঙ্গে সবার পার্থক্য কী থাকে?
সুতরাং, রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন “আমরা সবাই রাজা”, তখনই আসে নৈরাজ্যের প্রশ্ন। কেননা যে রাজ্যে বা যে রাষ্ট্রে এক ‘রাজা’ ছাড়া আর কারোর অস্তিত্বের, বিদ্যমানতার, বিরাজমানতার স্বীকৃতিই নেই, সেই রাজ্য দিয়ে কার লাভ? শুধু রাজাদের লাভ। এ কথা কে না জানে, রাজতন্ত্রের সর্বনিম্নপদস্থ দায়োয়ানটিও স্থানকালপাত্র নিজের মতো নিজেই খোদ রাজা; আগাপাছতলা এই রাজাদের সিস্টেম বা বন্দোবস্ত বা তন্ত্রের নামই তো দাঁড়িয়েছে রাজতন্ত্র। রাজতন্ত্রে দাসত্ব ছাড়া আমাদের জন্য কিছু বরাদ্দ নেই। রাজাকে দেশ লিখে দাও, তারপর দেশের মালিক রাজাকে খাজনা দাও, আর রাজপেয়াদার লাঠির বাড়ি খাও– এই আমাদের দায়িত্ব-কর্তব্য। তাহলে তো নৈরাজ্যই ভালো। রাজতন্ত্রের বদলে অরাজতন্ত্রই ভালো।
‘রাষ্ট্র’ শব্দের উৎপত্তিও ওই একই জায়গা থেকে–’রাজ’ (হরিচরণ)। রাষ্ট্র শব্দটির গোড়ায় আছে: “রাজ + ত্র (স্ট্রন)”, যার অর্থ “রাজ্য”। আর এই যে ‘স্ট্র’ –এর অর্থ সবসময়ই কোনোকিছুর গঠন-পরিগঠনের সঙ্গে যুক্ত। মানে রাজত্ব বা বিরাজত্ব জিনিসটার যে গাঠনিক কাঠামো, তারই নাম ‘রাষ্ট্র’। আবার, ‘রাষ্ট্র’ কথাটার আরও একটা অর্থ ‘প্রচার, প্রকাশ’ (হরিচরণ)। রাজার বিরাজত্ব যখন প্রচারিত হয়, প্রকাশিত হয় এবং সবাই সে ব্যাপারে সম্মত হয়, তখনই ‘রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে, গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে যায়। এই গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে যাওয়ার সঙ্গেই উপরের ওই ‘এ’ কথাটার সম্পর্ক। ‘এ’ অর্থ ‘তরণ-রহন (এখনি তরিত হয়ে অন্য কোথাও চলে যাব, এই ভাব) (২০০৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত কলিম খান এবং রবি চক্রবর্তীর ‘বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ” (ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থের অভিধান) পৃ. ৪৮৮]। তার মানে হলে, রাজা’-র একক, অদ্বিতীয় ও প্রশ্নাতীত বিরাজত্ব যখন বাকি সবাইকে ‘তরিত হয়ে কোথাও ‘রহন করে বা রহে বা স্থিতি-কাঠামো লাভ করে, তখনই তার নাম হয় রাষ্ট্র।
‘রাষ্ট্র’ জিনিসটা তার মানে নিতান্তই রাজা’-র একক ও অদ্বিতীয় বিদ্যমানতার সংস্থা। এ জিনিস কখনো জনগণের হতে পারে না। অতএব, বিদ্যমান গঠন-কাঠামোয় ‘জনগণের রাষ্ট্র’ বলে কিছু হয় না। এইজন্যই রাষ্ট্র শব্দের আরও একটা অর্থ ‘উপদ্রব, মকরাদি, দুর্ভিক্ষ (হরিচরণ)। তথাপি সভ্যতা নামক গত পাঁচ হাজার বছরের রাজতন্ত্রে-শাসনতন্ত্রে ‘রাজা’ রাষ্ট্র প্রভৃতিকে এতটাই স্বাভাবিকভাবে দেখানো হয়েছে যে, এগুলো সব ডালভাত তো বটেই, আলো-জল-হাওয়ার মতো প্রশ্নাতীত প্রাকৃতিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে যেন।
আজকের ‘রাজতন্ত্র’-এর মালিক-গোলাম-পেয়াদা আর নবরত্নসভার রাজ-বুদ্ধিজীবীরা এতক্ষণে হয়তো বলেই ফেলেছেন— তো জনাব, দেশটা চলবে কী করে, চালাবেটা কে? প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞ-অজ্ঞ রাজাদের, তাঁদের বাঁচাকাচ্চাদের, বাচ্চা-রাজাদের বা রাজসন্তানদের এইরকম শিশুসুলভ প্রশ্নেরও সযত্ন উত্তর রচনা করতে হবে বৈকি। এবং সে উত্তর হতে হবে চিন্তারহিত সাবালকের উপযোগী। কেননা সে নিজে চিন্তা করবে না, খুঁজবে না, ভাববে না, শুধু মুখস্থ কথা বলবে এবং “উত্তম পশু’-র মতো কুলগুরু পুরুতঠাকুরের শেখানো গায়ত্রী মন্ত্র জপে যাবে, আর এক প্রশ্ন হাজারোভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে যাবে— রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে হবে তো, নইলে দেশটা চলবে কীভাবে?
তাকিয়ে দেখুন— খোদ এই মহাবিশ্বপ্রকৃতিকে পরিচালনা করার জন্য কী কোনো ব্যক্তি-রাজা লাগে? রাজতন্ত্র লাগে? থানা-পুলিশ-পাইক-পেয়াদা-উজির নাজির-হাকিম-হুঁকুম-কারাগার-মন্ত্রী-মিনিস্টার লাগে? লাগে না। এগুলো লাগে পদার্থ-শক্তি-প্রাণের সর্বোচ্চ অভিপ্রকাশ মানুষের বেলায়ই শুধু। বাঘ-ভাল্লুক শেয়াল-কুকুর-হঁদুরের যা লাগে না, শাসকদের তা লাগে। আশ্চর্য ঘটনা বটে। বনের রাজা সিংহ, অথবা মাছের রাজা ইলিশ থেকে শুরু করে বাতির রাজা ফিলিপস পর্যন্ত যত বানোয়াট কেচ্ছা যে নিছকই ‘রাজা’-র দীপ্তি বাড়ানোর বুদ্ধিবৃত্তিক ছলনা, সে কথা বোঝা কী এতই কষ্ট? প্রয়োজনে স্মরণ করুন লোক-ছড়ার ইঙ্গিত– “মাছের রাজা রুই, শাকের রাজা পুঁই, নারীর মধ্যে আমেনার মা, পুরুষের মধ্যে মুই”।
হ্যাঁ, ‘রাজা’ একটি অভ্যাসের নামই বটে। আনুষ্ঠানিক রাজতন্ত্র তো এখন বিলুপ্তপ্রায় পদার্থ। তার বদলে গণপতি গণেশের গণতন্ত্রের উত্থানের হাওয়া নতুন করে বইতে লেগেছে শ’ দুয়েক বছর ধরে। তথাপি তথাকথিত নিরক্ষর অশিক্ষিতদের জন্য মাতব্বর-চেয়ারম্যান তো লাগেই, সর্বোচ্চ শিক্ষালয়ের জন্যেও একজন বাদশাহি ভাইস-চ্যান্সেলরই লাগে। এতসব দীক্ষায়ন-প্রশিক্ষণ সত্ত্বেও কিন্তু রাজা’ এবং ‘রাজতন্ত্র’-র বৈধতা ও যুক্তিসিদ্ধতা সম্পর্কে খটকা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় না। মনের মধ্যে কোথায় একটা খচখচানি থেকেই যায়। খটকাটা একেবারে আদি থেকেই ছিল বৈকি। মহাভারত তার প্রমাণ। মহাভারতের যুদ্ধের পরে তাঁর সর্বগ্রহণযোগ্যতার কারণে সকলেই যুধিষ্ঠিরকে ‘রাজা’ হওয়ার জন্য অন্তহীন কাকুতি-মিনতি করেই চলেছিলেন। কিন্তু যুধিষ্ঠির ছিলেন অনড়। রাজা’ হতে চাননি তিনি মোটেও। তিনি বলছিলেন তিনি ধর্ম জগতের লোক, রাজা তিনি হতে পারবেন না। মহাভারতের ‘শান্তিপর্ব’-এর গোড়ায় অর্জুনকে তিনি বলছিলেন: “আমি রাজ্যলোলুপ হইয়াই পাপপঙ্কে লিপ্ত হইয়াছি। … অতএব আমি সমস্ত রাজ্যসম্পদ পরিত্যাগপূর্বক শোকদুঃখবিবর্জিত হইয়া অরণ্যে গমন করিব। আমার রাজ্য বা উপভোগ্য দ্রব্যে কিছুমাত্র অভিলাশ নাই। অতঃপর তুমিই নির্বিঘ্নে এই পৃথিবী শাসন করো।”
যুধিষ্ঠিরের এই একান্ত উপলব্ধির উত্তরে নিতান্তই রুষ্ট অর্জুনের বক্তব্য ছিল খুবই আক্রমণাত্মক ও সুস্পষ্ট এবং তাতে চিরন্তন ক্ষত্রিয়ধর্ম তথা কর্তৃত্বধর্মের মহাসারকথাই ফুটে ওঠে –“যদি রাজধর্মে দ্বেষ প্রকাশ করিয়া আলস্যে কালহরণ করিবেন, তবে কি নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় বীরগণকে বিনাশ করিলেন? ক্ষাত্রধর্মাবলম্বী ব্যক্তিরা মিত্রের প্রতিও ক্ষমা, অনুকম্পা, কারুণ্য বা অনৃশংসতা প্রকাশ করেন না। … ক্ষত্রিয়গণ হিংসাৰ্থই জন্মগ্রহণ করেন। হিংসাই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন, সুতরাং সেই সহজ-হিংসাধর্মের ও তাঁহার সৃষ্টিকর্তার নিন্দা করা ক্ষত্রিয়ের নিতান্ত অকর্তব্য।” (মহাভারত, ২০০১ সালে প্রকাশিত কলকাতার ‘তুলিকলম প্রকাশনী’-র রাজ-সংস্করণ)।
ক্ষত্রিয়/শাসক/রাজনীতিবিদ এবং তাঁদের শাসনযন্ত্র তো আজকের দিনেও এমনকি বন্ধুর প্রতিও “ক্ষমা, অনুকম্পা, কারুণ্য বা অনৃশংসতা” প্রকাশ করে, তা তো সমকালীন জাতীয় আন্তর্জাতিক রাজনীতির দিকে তাকালেই জলজ্যান্ত বোঝা যায়। রাজনীতিতে চিরস্থায়ী শত্রু-মিত্র বলে কিছু নেই’ জাতীয় কথা তো আর এমনিতেই রটেনি! আদি ক্ষত্রিয় অর্জুন থেকেই এইসব ধারণার উৎপত্তি। কিন্তু যুধিষ্ঠির তাঁর কথায় অনড়। রাজা হওয়ার যুক্তিপ্রণালী কিছুতেই তাঁর গ্রাহ্য হয় না –হওয়ার কথা না বলেই।
শেষপর্যন্ত রাজ-রাজত্বের যুক্তিসিদ্ধতা কীসের উপরে দাঁড়াচ্ছে সেটাই আপাতত আমাদের দেখার বিষয়। তো অর্জুনের যে নিজের ক্ষত্রিয়ধর্ম নিয়ে গর্ব, সেই গর্ব নিয়ে ‘দেবত্ব’ অর্জন করা যায় না, ‘দেবলোকে’ যাওয়া যায় না, সে কথাই তুলে ধরেন যুধিষ্ঠির। অনেক অনেক কথার পর অর্জুনকে এক পর্যায়ে তিনি বলেন– “যে ভূমিপতি এই অখিল ভূমণ্ডল মধ্যে একাধিপত্য বিস্তার করেন, তাঁহারও এক ভিন্ন দ্বিতীয় উদর নাই। তবে তুমি কি নিমিত্ত বিপুল রাজ্যভোগের প্রশংসা করিতেছ? … অতএব তুমি অগ্রে উদরকে পরাজিত করো, তাহা হইলেই তোমার সমুদয় পৃথিবী পরাজয় করা হইবে। … রাজ্যালাভ ও রাজ্যরক্ষা এই উভয়েই ধর্ম ও অধর্ম আছে, অতএব উহা পরিত্যাগ করিয়া মহম্ভার হইতে বিমুক্ত হও। … যাহাদের বর্ণ ও আশ্রমাদির অভিমান থাকে, তাঁহারা পিতৃলোক, আর যাহারা অভিমানশূন্য, তাহারা দেবলোকে গমন করিয়া থাকে।”
কী সাংঘাতিক কথা। দেখা যাচ্ছে, বর্ণপ্রথার শ্রেষ্ঠত্বের ধারণার উপর দাঁড়িয়ে আছে যে রাজতন্ত্র, খোদ সেই “বর্ণ ও আশ্রমের অভিমান” যুধিষ্ঠির আর বহন করতে প্রস্তুত নন। আর এই অভিমান না-থাকলে যে ‘রাজত্ব’-ই অর্জন করতে পারে না, সেই গুরুতর সত্যের প্রতিও এভাবে তিনি বিকালের মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে বসে থাকেন। রাজত্ব’ অর্জনের চেয়ে ‘দেবত্ব অর্জনের দিকেই তাঁর ঝোঁক। ফলত তাঁর শোক, আক্ষেপ, অনুতাপ ও পাপবোধ কিছুতেই প্রশমিত হয় না, বারংবার উথলে উঠতে থাকে। বেদব্যাসের কাছে তিনি অতঃপর এই ভয়াবহ সত্য উচ্চারণ করতে ছাড়েন না যে, ‘রাজা’ এবং ধর্ম, ‘রাজত্ব’ ও ‘ধর্মবোধ’ আসলে পরস্পরের বিরোধী –“ধর্মচর্যা ও রাজ্যরক্ষা এই উভয় পরস্পর বিরুদ্ধ, অতএব এক ব্যক্তি কীরূপে ধর্মরক্ষা ও রাজ্যভার গ্রহণ করিতে পারে, নিরন্তর এই চিন্তা করিয়া আমি মোহে বারংবার অভিভূত হইতেছি।”
নকুল-সহদেব-দ্রৌপদী-ভীমের এবং ঋষি দেবস্থান ও মহর্ষি ব্যাসদেবের এবং সর্বোপরি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের বহু বহু প্রকার, উপযুপরি, অনুরোধ-উপরোধ-যুক্তি তর্ক-দৃষ্টান্ত ও উত্তেজনা-উক্তি এবং বিশেষত মহর্ষি বৈশম্পায়ন বেদব্যাস কর্তৃক প্রায়শ্চিত্ত পাওয়ার উপায় বর্ণনার পর যুধিষ্ঠির অবশ্য রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হন। কিন্তু সংশয় শোক তাঁর পিছু ছাড়ে না কিছুতেই। তখন বহু কিছুর পর মহর্ষি বৈশম্পায়নের পরামর্শে সবাই মিলে তাঁকে নিয়ে যান ‘সর্বজ্ঞ ধর্মবেত্তা’ “কুরুকুলপিতামহ বৃদ্ধ ভীষ্মের নিকট’ যুধিষ্ঠিরের ‘ধর্মগত সংশয় নিরাকরণ’ করার জন্য, সবিস্তারে রাজধর্ম সম্পর্কে জানার জন্য। সেখানে ভীষ্ম কর্তৃক নানারকম রাজধর্মবন্দনা এবং রাজার কর্তব্য-অকর্তব্য প্রভৃতি শোনার পরও যুধিষ্ঠির সংশয়মুক্ত হন না; বরং তিনি এবার সেই মোক্ষম, একেবারে গোড়ার প্রশ্নটি উত্থাপন করেন– “পিতামহ! রাজা’ এই শব্দটি কীরূপে সমুৎপন্ন হইল? রাজার হস্ত, গ্রীবা, পৃষ্ঠ, মুখ, উদর, শুক্র, অস্থি, মজ্জা, মাংস, রক্ত, নিঃশ্বাস, উচ্ছ্বাস, প্রাণ, শরীর, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, সুখ, দুঃখ, জন্ম ও মরণ যেরূপ, প্রজাগণেরও তদ্রূপ। তবে রাজা কীরূপে একাকী অসংখ্য বিশিষ্টবুদ্ধি মহাবলপরাক্রান্ত পুরুষের উপর আধিপত্য করিয়া সমুদয় পৃথিবী পালন করিতে সমর্থ হয়েন? সকল লোকে কি নিমিত্ত রাজার প্রসাদলাভের আকাঙ্ক্ষা করে?” এ প্রশ্ন তো চিরন্তন স্বাধীনতাপরায়ণেরই বটে। ‘রাজা’র এবং প্রজা’-র মধ্যে কী এমন দৈহিক-প্রাকৃতিক পার্থক্য আছে যে, একজন মাত্র ব্যক্তি কোটি কোটি মানুষের ‘রাজা হয়ে বসে থাকেন? আর লোকে তাঁকে মানেই-বা কী কারণে? গুরুতর এই প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্মদেব কিছুই লুকান না, ফাঁস করে দেন রাজতন্ত্রের গোড়ার গুমোর।
একটু ভিন্ন আঙ্গিকে হলেও, এমনকি ‘রাজা’-দের দিক থেকে হলেও মহাজ্ঞানী ভীষ্মদেব সেই স্মৃতিকথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বয়ান করেন কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ-পরবর্তী কলিযুগের আদি রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে। এই পৃথিবীর আদিতে যে অরাজ ছিল তার এবং সেই অরাজকে বলপ্রয়োগ ও শাস্ত্রপ্রয়োগের মাধ্যমে উচ্ছেদ করে প্রতিষ্ঠিত হয় নয়া রাজতন্ত্রের, আদি বৃত্তান্ত।
ভীষ্মদেবের কথায় যা বোঝা গেল : আদি সেই অরাজকে ভেঙে ফেলে দেবতারা যে আদি দেবতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন তা ছিল মনুষ্যশ্রমনির্ভর। মানুষের প্রদত্ত ‘হোমাদি’ স্বরূপ অন্নেই দেবতাদের গ্রাসাচ্ছাদন হতে এবং সেটাকেই দেবতারা বেদের নাম দিয়ে ‘ধর্ম’ বলে অনেক দিন পর্যন্ত চালিয়েছেন। কিন্তু মনুষ্যসমাজ এক পর্যায়ে যখন তা আর মানল না, তখন দেবকুলের মুখে এই মর্মে অন্নাভাবের হাহাকার শোনা গেল— নরলোকে আর বেদ নাই; নরলোকে আর ধর্ম নাই; সব বিনষ্ট হয়ে গেছে; মানবদিগের ক্রিয়াকলাপ উচ্ছিন্ন হওয়াতে আমাদিগের অন্নাভাব হইয়াছে’; শুধু তাই নয়, সেই অন্নাভাবের পরিণামে দেবতারা আর দেবত্বই বজায় রাখতে পারছেন না বলে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে আক্ষেপ করছেন –“অতঃপর আমরা মনুষ্যের ন্যায় অবস্থাপ্রাপ্ত হইলাম”।
মাঝখানে একটু টুকে রাখি– ‘দেবত্ব’ বা বৈষম্য টিকিয়ে রাখার শর্তই হচ্ছে ‘প্রিভিলেজ’ বা বিশেষাধিকারতন্ত্র, অর্থাৎ অন্যের (মানুষের) শ্রমে বসে বসে খাওয়া। বসে খাওয়ার বিশেষ অধিকার’ না-থাকলে দেবতাও আর দেবতা থাকেন না, তাঁর অন্নাভাব ঘটে, তিনি মনুষ্যদশাপ্রাপ্ত হন।
তো, ব্রহ্মা যেন নরলোক থেকে বেদ ও ধর্ম ধ্বংস হতে না দেন; একটা কিছু উপায় যেন তিনি বুদ্ধি খাঁটিয়ে, ‘স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে বের করেন –দেবতাগণের এই সম্মিলিত নালিশ এবং আহাজারির মুখে ব্রহ্মা তাঁদের আশ্বস্ত করেন— নো টেনশন, মুনষ্যজাতিকে আবার বেদ ও ধর্ম মানতে বাধ্য করা হবে। কিন্তু কীভাবে? রাজাপ্রথার জোরে, রাজতন্ত্রের জোরে। কিন্তু রাজতন্ত্র চলবে কীসের জোরে? রাজতন্ত্র চলে কীসের জোরে? কেন– শাস্ত্রের জোরে! স্বয়ং ব্রহ্মা সে উপায় বের করেন ‘বুদ্ধিবলে। আদিতম ‘শাস্ত্র’ রচনা করে বসেন ‘প্রজাপতি ব্রহ্মা –সৃষ্টি করেন তিনি প্রকৃষ্টরূপে জাত’ বিশেষ ধরনের মানুষকে যারা অতঃপর ‘প্রজা’ হিসাবে পরিচিত হবে।
আদিতম ‘শাস্ত্র’ আর ‘বুদ্ধিজীবী’-র সন্ধান তাহলে মহাভারতেই পাওয়া গেল –| তিনি খোদ ব্রহ্মা। জানা গেল— তাঁর কাজ হচ্ছে শাসকদের অনুকূলে বৈষম্য ও বিশোধিকারতন্ত্র টিকিয়ে রাখা –প্রজাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে এবং তাতে কাজ না-হলে শাস্ত্রের জোর, শাস্তির জোর ও ভয়ের জোর খাটানোর ‘প্রেসক্রিপশন’ দিয়ে। এভাবে অবশেষে বুদ্ধির জোরে এবং গায়ের জোরে দুর্দান্ত ও দুর্দমনীয় মানুষকে শান্ত ও দমিত করার ব্যবস্থা হলে— তাঁদেরকে এই পৃথিবীতে রাজার রাজত্ব মানানো হলে, রাজবশীভূত করা হলে আদিতম শাস্ত্রের জোরে এবং ‘দণ্ড’-ই হচ্ছে এই ভূভারতের আদিতম শাস্ত্র। আর সেই শাস্ত্র চলে রাজা এবং রাজবুদ্ধিজীবীর যুগলবন্দিতে। এবার সেই চাঞ্চল্যকর ইতিহাসের সার-বিবরণী হুবহু শোনা যাক কুরুকুলপিতামহ সর্বজ্ঞ বৃদ্ধ ভীষ্মের মুখে।
ভীষ্ম কহিলেন, “ধর্মরাজ! সত্যযুগে প্রথমে যেরূপে রাজত্বের সৃষ্টি হয়, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ করো। সর্বপ্রথমে পৃথিবীতে রাজ্য, রাজা, দণ্ড বা দপ্তাহ ব্যক্তি কিছুই ছিল না। মনুষ্যেরা একমাত্র ধর্ম অবলম্বনপূর্বক পরস্পরকে রক্ষা করিত। মানবগণ এইরূপে কিছুদিন কালযাপন করিয়া পরিশেষে পরস্পরের রক্ষণাবেক্ষণ নিতান্ত কষ্টকর বোধ করিতে লাগিল। ওই সময় মোহ তাহাদিগের মনোমন্দিরে প্রবিষ্ট হইল। মোহের আবির্ভাববশত ক্রমশ জ্ঞান ও ধর্মের লোপ হইতে লাগিল এবং মানবগণ ক্রমে ক্রমে লোভপরতন্ত্র, পরধনগ্রহণতৎপর, কামপরায়ণ, বিষয়াসক্ত ও কাৰ্যাকাৰ্য্যবিবেকশূন্য হইয়া উঠিল। … নরলোক এইরূপে কুমার্গগামী হইলে বেদ বিনষ্ট ও ধর্ম এককালে বিলুপ্ত হইয়া গেল।
তখন দেবগণ নিতান্ত শঙ্কিতচিত্তে লোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, “ভগবন্! লোভমোহাদি প্রভৃতি নীচবৃত্তিসমুদয় নরলোকস্থ সনাতন বেদ গ্রাস করাতে আমরা ভীত হইয়াছি। বেদ ধ্বংস হওয়াতে ধর্মও বিনষ্ট হইয়াছে। অতঃপর আমরা মনুষ্যের ন্যায় অবস্থাপ্রাপ্ত হইলাম। মানবগণ হোমাদি কার্য দ্বারা ঊৰ্দ্ধবর্ষী বলিয়া বিখ্যাত ছিল এবং আমরা বারিবর্ষণাদি দ্বারা অধোবর্ষী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলাম; কিন্তু এক্ষণে মানবদিগের ক্রিয়াকলাপ উচ্ছিন্ন হওয়াতে আমাদিগের অন্নাভাব হইয়াছে। অতএব যাহাতে আপনার প্রভাবে সম্ভত এই প্রাকৃতিক নিয়ম ধ্বংস না হয়, আপনি স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে তাহার সদুপায় উদ্ভাবন করুন।’
তখন ভগবান্ কমলযোনি (ব্রহ্মা) সুরগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, “হে দেবগণ! তোমরা ভীত হইও না; আমি অচিরাত উহার উপায় চিন্তা করিতেছি।” প্রজাপতি দেবগণকে এই কথা বলে বুদ্ধিবলে একটি লক্ষ অধ্যায়যুক্ত নীতিশাস্ত্র রচনা করলেন। …ভগবান্ পদ্মযোনি ওই নীতিশাস্ত্র প্রণীত করিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে হৃষ্টমনে কহিলেন, “সুরগণ! আমি ত্রিবর্গ সংস্থাপন ও লোকের উপকার-সাধনের নিমিত্ত বাক্যের সারস্বরূপ এই নীতিশাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছি। ইহা পাঠ করিলে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ দর্শনপূর্বক লোকরক্ষা করিবার বুদ্ধি জন্মিবে। এই শাস্ত্র দ্বারা জগতের যাবতীয় লোক দণ্ডপ্রভাবে পুরুষার্থ ফলোভে সমর্থ হইবে; অতএব ইহার নাম দণ্ডনীতি হইল।”
এতটা সুস্পষ্ট কথা আর কী হতে পারে। পরিষ্কারভাবেই দেখা যাচ্ছে, ভূভারতের আদিতম নীতিশাস্ত্রটি হল ‘দণ্ডনীতি’ এবং যুধিষ্ঠিরকে পিতামহ ভীষ্মদেব আরও বলেছিলেন, “দণ্ডপ্রভাবেই জনসমাজে নীতি ও ধর্মের প্রচার হইয়াছে”। তার মানে, ‘দণ্ডনীতি’-ই যে কতৃত্বতন্ত্রের আদিতম নীতিশাস্ত্র শুধু তাই-ই নয়, এ জিনিস জনসমাজে প্রচলিত নীতিবোধের জনকও বটে। এবং এই নীতিবোধের প্রধান দুই উপায় হচ্ছে ‘নিগ্রহ’ ও ‘অনুগ্রহ’। এই হল সেই ‘নিমিত্ত’, যে নিমিত্তে “সকল লোকে … রাজার প্রসাদলাভের আকাঙ্ক্ষা করে”। নইলে যে মার খেতে হবে, নিগৃহীত হতে হবে। তার চেয়ে অনুগ্রহ-তাড়নাই বাস্তববাচিত।
দণ্ডনীতি কী বস্তু, সমাজ-সংসারে এর কাজ কী তাও যুধিষ্ঠিরকে সবিস্তারে বুঝিয়ে বলেছিলেন অর্জুন– “দণ্ড প্ৰজাদিগকে শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। সকলে নিদ্রায় অভিভূত হইলেও দণ্ড একাকী জাগরিত থাকে। পণ্ডিতেরা দণ্ডকে প্রধান ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন”।
এসব কথা আজকের সংসদীয় গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের অত্যাধুনিক প্রবক্তাদের মুখে শোনাও যা, ‘সভ্যতার উষালগ্নের দণ্ড বা আইন প্রয়োগকারী সত্তা অর্জুনের মুখে শোনাও তা-ই। কেননা আইনের শাসন তথা দণ্ডনীতি প্রতিষ্ঠার নামই সভ্যতা’ এবং সত্যিকারের ‘সভ্যতার’ নামে এই জিনিসই চলছে গত পাঁচ হাজার বছরের ‘কতৃর্তৃতান্ত্রিক সভ্যতা’ জুড়ে। এই দণ্ডনির্ভর সভ্যতায় দণ্ডই ‘প্রধান ধর্ম’ বটে, তবে তা ‘মনুষ্যধর্ম’ নয়। শাস্ত্রধর্ম তথা ‘রাজধর্ম এবং সেই কারণেই বিপরীত দিক থেকে ‘প্রজা’-র ধর্মও বটে। অন্য কথায় এ বস্তুই আজকের ‘সভ্যযুগের রাষ্ট্রের ধর্ম। আইনের ধর্মই তো দণ্ড। শাসনের ধর্মই তো দণ্ড। এই আইনের শাসনকে কখনও সত্যিকারের মনুষ্যধর্মের নামে চালানো যায় না। একে চালাতে হয় শাস্ত্রধর্মের নামে। এবং পুনরাবৃত্তি করতেই হবে, আদিতম শাস্ত্রধর্মের নামই দণ্ডশাস্ত্র বা দণ্ডধর্ম বা কর্তৃত্বনীতি বা কর্তৃত্বধর্ম। এই জিনিসটিকেই কর্তৃত্বতন্ত্র মানুষের ধর্ম এবং প্রকৃতির ধর্ম বলে চালাতে চায়।
যুধিষ্ঠিরকে অর্জুন বলছেন, “ভয়ের রাজত্বই হচ্ছে দণ্ডনীতির প্রাণ” এবং “দণ্ডপ্রভাবে ধন ও ধান্য রক্ষিত হয়। … অনেকানেক পাপপরায়ণ পামরেরা রাজদণ্ডভয়ে, অনেকে যমদণ্ডভয়ে, অনেকে পরলোকভয়ে এবং অনেকে লোকভয়ে পাপানুষ্ঠান করিতে পারে না। অনেকে কেবল দণ্ডভয়েই পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করে না। ফলত সংসারে প্রায় সমুদয় কাৰ্য্যই দণ্ডভয়ে নির্বাহ হইতেছে। … ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক ইহারা দণ্ডের ভয়ে স্ব স্ব পথে অবস্থান করিতেছেন। ভীত না হইলে কেহই যজ্ঞানুষ্ঠান, দান ও নিয়ম প্রতিপালন করিতে ইচ্ছা করে না।” তৎকালীন প্রধান সেনাপতি অর্জুনের বক্তব্য খুবই পরিষ্কার। দণ্ডনীতি মানেই হচ্ছে দমননীতি এবং শাসন-ত্রাসনের নীতি : “দমন ও শাসন করে বলিয়াই উহা দণ্ড নামে নির্দিষ্ট হইয়াছে”। আর কার জন্য কোন্ দণ্ড সমুচিত তার মোক্ষম বিধানও প্রস্তুত— “দণ্ড সংসার রক্ষা না করিলে সমুদয়ই গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হইত। দণ্ড দুর্দান্তদিগকে দমন ও দুর্বিনীত ব্যক্তিদিগকে শাসন করিয়া থাকে। দমন ও শাসন করে বলিয়াই উহা দণ্ড নামে নির্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণের তিরস্কার, ক্ষত্রিয়ের বেতন প্রদান না করা, বৈশ্যের রাজসমীপে দ্রব্যজাত সমর্পণ এবং শূদ্রের সর্বস্বাপহরণই সমুচিত দণ্ড।”
কী সুনির্দিষ্ট, কী তীব্ৰসূচিমুখ এই দণ্ডনীতি সেই প্রাচীনকাল থেকেই। আর শাসনের প্রশ্নে সে কাউকেই ছাড়ে না। শাসনযন্ত্রের হাতে তথা শাসকের হাতে, রাষ্ট্রযন্ত্রের ম্যানেজারদের হাতে ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র পর্যন্ত কারও কোনো নিস্তার নেই? পার্থক্য আছে বৈকি। ব্রাহ্মণের জন্য তিরস্কার’-ই যথেষ্ট। আর শূদ্রকে শায়েস্তা করার জন্য চাই তার সর্বস্ব অপহরণ করা। (সেলিম রেজা নিউটন)।
প্রাক-ঐতিহাসিককালে মানুষের আত্মরক্ষার প্রধান উপকরণ ছিল দণ্ড। এক্কেবারে প্রথমদিকে ছিল শক্ত কাঠের লাঠি, পরবর্তী সময়ে হাড় বা ধাতুর তৈরি দণ্ড বা অস্ত্র। লগুড়, গাছের গুঁড়ি, বীণার ছড়, যষ্টি, নৌকার দাঁড় লাঙলের ঈষ, হাত বা ভুজ– সবই দণ্ড। সুস্থিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাজদণ্ড হল আইন ও বিচারের প্রতীক। জগতের সকলকে এ দমন করে, শাসন বা সংযত করে –তাই এর নাম দণ্ড। তাই শাসক হলেন দণ্ডধারী বা দণ্ডধর বা দণ্ডপাণি। মনু বলেছেন –লঘু পাপে লঘু দণ্ড, গুরু পাপে গুরু দণ্ড। দণ্ড বিধান এবং দণ্ড প্রণয়ন রাষ্ট্রনায়কের অন্যতম কর্তব্য।
মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ের ১৮ নম্বর শ্লোকে মনু বলছেন –”দণ্ড শাস্তি প্রজাঃ সর্বা এবাভিরক্ষতি।/দণ্ড সুপ্তেম্ভ জাগর্তি দণ্ডং ধর্মং বিদূর্বধাঃ।” অর্থাৎ দণ্ডই প্রজাদের শাসন করে, দণ্ডই তাদের রক্ষা করে, রক্ষক পুরুষেরা নিদ্রিত থাকলে দণ্ডই জেগে থাকে। পণ্ডিতগণ দণ্ডকেই ধর্ম বলে জানেন। অপরদিকে দণ্ড না-থাকলে কী হত সে বিষয়েও মনু বলেছেন –“যদি ন প্রণয়েদ্রাজা দণ্ডং দণ্ডেম্বততিঃ।/শূলে মৎসানিবাপক্ষ্য দূর্বলান বলবত্তরা।” (মনুসংহিতা– সপ্তম অধায়– শ্লোক ২০) অর্থাৎ রাজা যদি অনলসভাবে দণ্ডনীয় ব্যক্তির দণ্ডবিধান না করতেন, তবে শূলে মৎস্যের ন্যায় বলবান ব্যক্তিরা দুর্বল ব্যক্তিগণকে উৎপীড়ন করত। আরও যা যা ঘটত সেগুলিও মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ের ২১ নম্বর শ্লোকে উল্লেখ আছে– “অদ্যাৎ কাকঃ পুরোশং শ্বাবলিহাদ্ধবিস্তথা।/স্বামঞ্চ ন স্যাৎ কস্মিংশ্চিৎ প্রবর্তেধরোত্তরম্।” অর্থাৎ দণ্ড না-হলে কাক যজ্ঞীয় পিঠা ভক্ষণ করত, কুকুর যজ্ঞীয় হবি লেহন করত এবং কারও কোনো বিষয়ে অধিকার থাকত না। এক ওলট-পালট অবস্থার সৃষ্টি হত। মনু মনে করেন, “সর্বো দণ্ডজিততা লোকো দুর্লভভা হি শুচিনরঃ।/দণ্ডস্য হি ভয়াৎ সর্বং জগদ্ভোগায় কল্পতে।” (মনুসংহিতা– সপ্তম অধ্যায়– শ্লোক ২২) অর্থাৎ দণ্ডের দ্বারাই সকল মানুষ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, কারণ স্বভাবশুচি লোক দুর্লভ। দণ্ডেরই ভয়ে সমগ্র জগৎ ভোগে সমর্থ হয়।
আগেই উল্লেখ করেছি লঘু পাপে লঘু দণ্ড, গুরু পাপে গুরু দণ্ড। কোন্ অপরাধ লঘু কোন্ অপরাধ গুরু, তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়। শাস্তির ধরনও বদলে যায়। এ বড়ো আপেক্ষিক ব্যাপার। কোন্ অন্যায়ের কোন্ শাস্তি হবে তা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট সেই রাষ্ট্রের আইন ব্যবস্থার উপর, যা শাসক দ্বারা নির্দেশিত। লঘু পাপেও যে গুরু দণ্ড দেওয়া হয় এমন উদাহরণ ঝুড়ি ঝুড়ি আছে। প্রাচীন ভারতে ভয়ংকর আঘাতে তাৎক্ষণিক মৃত্যু এবং অন্যান্য গুরুতর অপরাধ –যেমন বাবা-মা-ভাই-বোন-শিক্ষক-গুরু এবং সন্ন্যাসী বা তপস্বীর মৃত্যু ঘটালে আগুনে পুড়িয়ে অথবা জলে ডুবিয়ে অথবা বিষ খাইয়ে মৃত্যুদণ্ড প্রযুক্ত হত। প্রাচীন রোমেও পিতৃহত্যা, স্বজনহত্যা বা রাজহত্যার অপরাধীকে বুনো কুকুর বা বিষধর সাপের সঙ্গে থলির মধ্যে ঢুকিয়ে হত্যা করা হত। ১৭৯৫-৫০ খ্রিস্টপূর্বে হামুরাবির আইন অনুসারে ব্যাবিলনে বিক্রেতা যদি মদ বিক্রিতে মাপে কম দিত তাহলে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হত। প্রাচীন ভারতে নরহত্যা ছাড়া যেসব অপরাধে মৃত্যুদণ্ড হত, তার মধ্যে আছে –রাজদ্রোহ, মানী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে অপহরণ– বিশেষত নারীহরণ, উচ্চবর্ণের স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ যৌন সম্পর্ক, রাজাদেশ জাল বা নকল করা, চুরি ও চোরাই মালসহ ধরা পড়া, রাজকোশ থেকে মণিমাণিক্য চুরি, চাষের জন্য তৈরি বাঁধ বা সেতু নষ্ট করা, রাজার হাতি-ঘোড়া-রথ চুরি করা, ঘরবাড়ি বা খেতখামারে আগুন লাগানো, মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীর মৃতদেহ সৎকার করা ইত্যাদি। এখানেই শেষ নয়– বৈদিক ও পরবর্তী যুগে ব্রাহ্মণ ছিল অবধ্য। ব্রাহ্মণগণ প্রাণদণ্ডাই কোনো অপরাধ করলে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে দেশ থেকে নির্বাসন দেওয়া হত। তখনকার সময়ে ‘দেশ’ বলতে ভারত বহির্ভূত বোঝত না, বোঝাত অন্য রাজ্য। অর্থাৎ কাম্পিল্যের নির্বাসিত ব্রাহ্মণ আরামসে মগধে বসবাস করতে কোনো অসুবিধা ছিল না। প্রাচীন গ্রিসেও ‘nobleman’-দের ক্ষেত্রেও মৃত্যুদণ্ডের বদলে নির্বাসন দেওয়া হত। তবে সেই নির্বাসিত ব্যক্তিটি যদি পুনরায় রাষ্ট্রে প্রবেশ করে তাঁর সম্পত্তি হরণ করে প্রাণদণ্ড দেওয়া হত। তবে প্রাচীন ভারতে শূদ্ররাই বেশি শাস্তি ভোগ করত। শূদ্রদের তুলনায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের মৃত্যুদণ্ড কমই হত।
শাস্তির নামে মানুষ যে কত নৃশংস হত করে তার নমুনা ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে। হত্যার ইতিহাসে রক্তাক্ত হয়ে আছে মানুষের সভ্যতা। ধমকে, দাবিয়ে রাখার সভ্যতা। শুষে খাওয়ার সভ্যতা। ছোটো মাছকে গিলে খাওয়ার সভ্যতা। শাস্তি কেন দেওয়া হত? ‘সবক’ শেখানোর জন্য? বিশ্বাস করি না। মৃত্যুদণ্ড যিনি দেন, মৃত্যুদণ্ড যিনি কার্যকর করেন, মৃত্যুদণ্ডের মতো হত্যাকাণ্ড যে বা যাঁরা সমর্থন করে উল্লসিত হন তাঁরা প্রত্যেকেই হত্যাকারী। হত্যার সপক্ষে যাঁরা বক্তৃতা দেন, আসলে তাঁদের অন্তরের ভিতর হত্যার স্পৃহা জেগে থাকে। হ্যাঁ, অবচেতন মনে। দেশদ্রোহী হলে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে আছে অবশ্যই মৃত্যুদণ্ড। দেশদ্রোহী এবং দেশপ্রেমী –এই দুটি ভাগে ভাগ হয়ে যায় মানুষ। কেন? কে দেশদ্রোহী? কেই-বা দেশপ্রেমী? যদি কিষাণজি দেশদ্রোহী হন, যদি কাসভ দেশদ্রোহী হন, যদি আফজল গুরু দেশদ্রোহী হন– তবে ব্রিটিশ-ভারতে কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিসমিল ও রোশনলাল, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত গণেশ পিংলে ও কর্তার সিং, দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত বসন্ত বিশ্বাস, আলিপুর বোমা মামলায় ধৃত কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসু, পুনা কালেকটর হত্যার দায়ে ধৃত দামোদর চাপের ও বালকৃষ্ণ হরি চাপের প্রমুখ ব্যক্তিদের দেশদ্রোহী ও সন্ত্রাসবাদীদের কী বলবেন? সময়ের বিচারে তাঁরাও কিন্তু দেশদ্রোহীই। সে সময়কার রেকর্ডে তাঁদের নামের সঙ্গে ‘Terrorist’ উল্লেখ আছে।
বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী কর্তৃক গঠিত একটি আধাসামরিক বাহিনী। এটি অখণ্ড পাকিস্তানপন্থী বাঙালি এবং উর্দুভাষী অবাঙালি অভিবাসীদের নিয়ে গঠিত হয়। অবরুদ্ধ বাংলাদেশে স্বাধীনতার জন্যে লড়াইরত মুক্তিবাহিনীকে প্রতিরোধ করার জন্য ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে খুলনায় প্রথম রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়। পাকিস্তানের সংবিধানের প্রতি সত্যিকার আনুগত্য প্রদর্শন করে তাঁরা স্বাধীন বাংলাদেশের কাছে অপরাধী হলেও অখণ্ড পাকিস্তানের কাছে চরম আনুগত্য বইকি! রেজাকার বা রাজাকার মানে স্বেচ্ছাসেবী, এই রাজাকারেরা হলেন গোলাম আজম, আব্বাস আলি খান (জামাতে ইসলামী বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির), মতিউর রহমান নিজামী, আলি আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ (ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি এবং আলবদর বাহিনীর ঢাকা মহানগরীর প্রধান), মোঃ কামরুজ্জামান (জামাতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল), দেলোয়ার হোসেন সাঈদি (জামাতে ইসলামীর মজলিসের শুরার সদস্য), আবদুল কাদির মোল্লা (জামাতে ইসলামের প্রচার সম্পাদক), ফজলুল কাদের চৌধুরী, সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী– যাঁদের অখণ্ড পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য দেখানোর অভিযোগে অনেককেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। রেজাকার বা রাজাকার বাহিনী কোরান Šiau xtetet facua, “I shall bear true allegiance to the constitution of Pakistan as framed by law and shall defend Pakistan, if necessary, with my life.” অর্থাৎ, “আমি আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের সংবিধানের প্রতি সত্যিকার আনুগত্য প্রদর্শন করব এবং জীবন দিয়ে হলেও পাকিস্তানকে রক্ষা করব।” ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর তারিখের আগে যাঁরা ছিলেন পাকিস্তানের দেশপ্রেমী, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ডিসেম্বর তারিখের পর থেকে তাঁরাই দেশদ্রোহী হয়ে গেলেন। অসম সাহসিকতার জন্য যাঁদের পুরস্কার পাওয়ার কথা ছিল, তাঁদেরই কপালে জুটল মৃত্যুদণ্ড। অথচ ভাবুন তো, যদি কোনো কারণে মুক্তিযুদ্ধ সফল না হত এই কাদের মোল্লারাই অখণ্ড পাকিস্তানের ঘরে ঘরে দেশপ্রেমী হিসাবে পূজিত হতেন। তাই না?
১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগে ভারত কবে ভারতীয়দের ছিল? প্রায় ২০০ বছর ব্রিটিশরা শাসন করেছিল, ব্রিটিশদের ছিল। তার আগে প্রায় ৮০০ বছর মুসলিম শাসকরা শাসন করেছিল, তারও আগে বেদের যুগ পর্যন্ত ভারত বিদেশিদের কর্তৃক শাসিত হয়েছে। এমনকি যে আর্যদের নিয়ে আমাদের অহংকার, সেই আর্যরা কিন্তু ভারতের ভূমিপুত্র নন, ভারত বংশোদ্ভূতও নয়— বিদেশিই। তখন বিপ্লবীরা কোথায় ছিলেন? অত্যাচার কোন শাসক করেননি! তাহলে কার বা কাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ? দেশদ্রোহিতাই-বা কেন? ব্রিটিশ-ভারতে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীদের মৃত্যুদণ্ড যদি অনৈতিক হয়, অন্যদের ক্ষেত্রে সেটা উলটো হবে কেন? অর্থাৎ দেশদ্রোহিতা বা সন্ত্রাসবাদিতা যেহেতু দেশ-কাল বিশেষে আপেক্ষিক, সেই কারণে সেইসব কোনো ব্যক্তিদের মৃত্যুদণ্ডও মেনে নেওয়া যাচ্ছে না।
দেশপ্রেমের প্রসঙ্গে বলব, কারা দেশপ্রেমী? যাঁরা নানা ছলনায় কোটি কোটি টাকার আয়কর ফাঁকি দিয়ে রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতারণা করেন, তাঁরা দেশপ্রেমী? যেসব নিয়োগ কর্তৃপক্ষ শ্রমিক বা কর্মচারীদের রক্ত শুষে খায়, তাঁরা দেশপ্রেমী? যেসব শ্রমিক বা কর্মচারীরা নানা কায়দায় শ্রম চুরি করে, মালপত্র ঝেড়ে ফাঁক করে দেয়, তাঁরা দেশপ্রেমী? যে সব মাননীয় নাগরিকরা কালো টাকার পাহাড় জমান, তাঁরা দেশপ্রেমী? যেসব মাননীয় নাগরিকরা আয় বহির্ভূত প্রচুর অর্থ সুইস ব্যাঙ্কে জমা রেখে আসেন, তাঁরা দেশপ্রেমী? আয়কর দপ্তরের যেসব অসৎ অফিসারেরা অসৎ ব্যবসায়ীদের কোটি কোটি টাকার আয়কর ফাঁকি দেওয়ার সুযোগ করে দিয়ে নিজে ‘লাল’ হয়ে সরকারকে দিনের পর দিন ‘কালো’ করে চলেছেন, তাঁরা দেশপ্রেমী? যেসব নির্লজ্জ নাগরিকরা দেশের যত্রতত্র দাঁড়িয়ে পেচ্ছাব ছিটিয়ে দেশের সর্বত্র কলুষিত করেন, তাঁরা দেশপ্রেমী?
একদা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীকে জনসমক্ষে প্রকাশ্যে দণ্ড কার্যকর করা হত। সেক্ষেত্রে দণ্ড প্রয়োগের স্থান-সময় আগেভাগে জানিয়ে দেওয়া হত, যাতে সাধারণ মানুষ যত বেশি সংখ্যক উপস্থিত থাকতে পারে। উদ্দেশ্য : যাতে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষেরা অপরাধীর দণ্ড নিজের চোখে দেখে অপরাধ বিষয়ে তাঁর একটা বিরূপ মানসিক প্রতিক্রিয়া হয় এবং তাতে সামাজিক সুফল মিলবে। না, মৃত্যুদণ্ড দিয়ে এক ইঞ্চিও সামাজিক সুফল মেলেনি। হাজার হাজার বছর ধরে এত নৃশংস কঠোর শাস্তি দিয়েও পৃথিবীকে অপরাধমুক্ত করা যায়নি। অপরাধ হয়েই চলেছে এবং তা হাজারবার মৃত্যুদণ্ড দিয়েও অবস্থার পরিবর্তন করা যাবে না। কারণ প্রায় সব অপরাধের পিছনে থাকে আর্থ-সামাজিক সংকট এবং মানসিক বৈকল্য, যার দায় কোনো রাষ্ট্র এড়াতে পারে না।
মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধির হত্যাকাণ্ড উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গান্ধির হত্যাকারী ছিলেন তাঁর মতোই একজন উচ্চশ্রেণির ব্রাহ্মণ। তার নাম নাথুরাম গডসে। গান্ধি হত্যাকাণ্ডে গডসের যে যুক্তি ছিল তা তাঁর একার ছিল না। হিন্দুদের একটি বিরাট অংশ গডসের যুক্তি সঠিক বলে মনে করে। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই থেকে ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ছয়বার গান্ধিকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়। নাথুরাম গডসে ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বরে প্রথমবার গান্ধিকে হত্যার চেষ্টা করেন। ব্যর্থ হয়ে তিনি আবার ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারি একই চেষ্টা চালান। পরপর দু-বার ব্যর্থ হয়ে তৃতীয়বার ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে ৩০ জানুয়ারি তিনি সফল হন। তিনি মনে করতেন, অষ্টাদশ শতাব্দীতে মোগলদের বিরুদ্ধে মারাঠা দস্যু শিবাজি, রাজা রাবণের বিরুদ্ধে হিন্দু বীরদের সহিংস লড়াইয়ের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে অহিংস পথ অবলম্বন করে গান্ধি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেছেন। তাই তাঁকে হত্যা করা পুণ্যের কাজ। গডসে এ সিদ্ধান্তে আসেন যে, জাগতিক বিচারে তাঁর পরিণাম যাই হোক, পরজন্মে তিনি মুক্তি পাবেন। শুধু তাই নয়, গান্ধি হত্যাকাণ্ড সফল হলে তাঁর স্বধর্মের অনুসারী ভারতের ৩০ কোটি হিন্দুও অবিচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে। গান্ধি হত্যাকাণ্ডে এগুলোই ছিল নাথুরাম গডসের যুক্তি। তিনি মনে করতেন— শিবাজি, রানা প্রতাপ ও গুরু গোবিন্দের মতো ঐতিহাসিক বীর যোদ্ধাদের বিপথগামী দেশপ্রেমিক হিসাবে নিন্দা করে গান্ধিজি নিজের আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করেছেন। গান্ধিজি অহিংস ও সত্যাগ্রহ নীতির নামে দেশে অবর্ণনীয় দুর্দশা ডেকে এনেছেন। পক্ষান্তরে, রানা প্রতাপ, শিবাজি ও গুরুগোবিন্দ তাঁদের জাতিকে যে মুক্তি এনে দিয়েছিলেন সেজন্য তাঁরা জাতির হৃদয়ে চিরজাগরুক হয়ে থাকবেন। এই হল নাথুরাম গডসে।
মেরঠে নাথুরাম গডসের মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হবে বলা হয়েছিল অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে। হিন্দু মহাসভার সভাপতি শুধু জানিয়েছেন, মন্দিরে নাথুরাম গডসের সঙ্গে থাকবেন অখণ্ড ভারতমাতা। হিন্দু মহাসভার তরফে চন্দ্ৰপ্ৰকাশ কৌশিক বলেছেন, “মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে নাথুরাম গডসের কোনো ব্যক্তিগত দুশমনি ছিল না। তবুও তিনি গান্ধিজিকে খুন করেছিলেন। কেন সেই ঘটনা ঘটেছিল, তার তদন্তও হয়নি। কেন হয়নি, সেটা একটা প্রশ্ন। যদি আকবর রোড, হুমায়ুন রোড, ঔরঙ্গজেব রোড থাকে, তা হলে গডসের নামে কেন রাস্তা থাকবে না? কেন তাঁর একটি মূর্তি তৈরি হবে না।” অর্থাৎ, আপনার কাছে যে টেররিস্ট, আমার কাছে সে বিপ্লবী শহিদ। আপনার কাছে যে গড, আমার কাছে সে গডসে –এরকম ব্যাপার আর কি! মহাত্মা গান্ধির ঘাতক নাথুরাম গডসেকে ‘দেশপ্রেমিক’ বলেছিলেন বিজেপি সাংসদ সাক্ষী মহারাজ। সাক্ষী মহারাজ বলেন, “নাথুরাম গডসে একজন জাতীয়তাবাদী ছিলেন। মহাত্মা গান্ধি যতটা করেছেন দেশের জন্য, গডসের অবদানও ততটা।” পরে অবশ্য চাপে পড়ে সাক্ষী মহারাজ বলেন, “যদি ভুল করে কিছু বলে থাকি, তা হলে কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। নাথুরাম গডসে দেশপ্রেমিক নয়। কখনও ছিল না।” চাপে পড়ে ভুল স্বীকার করা আর শ্রদ্ধা থেকে সরে আসা এক ব্যাপার নয়। গডসের ফাঁসি হয়েছে একথা ঠিক। তবে তিনি যে চিন্তায় আলোড়িত হতেন সে চিন্তার মৃত্যু আজও হয়নি। এখনও ভারতের কট্টরপন্থী এবং উগ্রবাদী হিন্দু গডসের চিন্তা ও চেতনায় আলোড়িত হয়। তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।
রেহানা জাব্বারি। ইরানের এক নারীর নাম। ছাব্বিশ বর্ষীয় এই নারীকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। জানা গেছে তাঁকে ধর্ষণে চেষ্টাকারীর বুকে ছুরি বসানোর অপরাধে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয় ইরানের সুপ্রিম কোর্ট। ২৫ অক্টোবর তাঁর মত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। রেহানার ফাঁসির বিরোধিতা করে গোটা বিশ্বের অজস্র মানবাধিকার সংগঠন। প্রাণভিক্ষার আবেদন জানায় দুনিয়ার অনেক মানুষ। আর মেয়ের বদলে তাঁকেই ফাঁসিতে ঝোলানোর মিনতি করেছিলেন রেহানার মা শোলেহ। কিন্তু কোনো কিছুতেই কান দেয়নি সরকার। মৃত্যুর আগে তাঁর মাকে এক মর্মস্পর্শী চিঠি লিখে গেছেন রেহানা। মৃত্যুকে তিনি অভিহিত করেছেন নিয়তির বিধান হিসাবে। ফাঁসির পর তাঁর দেহাংশ দান করার অনুরোধ জানিয়েছেন জন্মদাত্রীকে। রেহানার সেই মর্মস্পর্শী চিঠি গণমাধ্যমের হাতে তুলে দিয়েছেন মানবাধিকার সংগঠন ও শান্তিকামী গোষ্ঠীর সদস্যরা।
“প্রিয় শোলেহ,
আজ জানতে পারলাম এবার আমার ‘কিসাস’ (ইরানের আইন ব্যবস্থায় কর্মফল বিষয়ক বিধি)-এর সম্মুখীন হওয়ার সময় হয়েছে। জীবনের শেষ পাতায় যে পৌঁছে গিয়েছি, তা তুমি নিজের মুখে আমায় জানাওনি ভেবে খারাপ লাগছে। তোমার কি মনে হয়নি যে এটা আমার আগেই জানা উচিত ছিল? তুমি দুঃখে ভেঙে পড়েছ জেনে ভীষণ লজ্জা পাচ্ছি। ফাঁসির আদেশ শোনার পর তোমার আর বাবার হাতে চুমু খেতে দাওনি কেন আমায়?
দুনিয়া আমায় ১৯ বছর বাঁচতে দিয়েছিল। কেননা সেই অভিশপ্ত রাতে আমারই তো মরে যাওয়া উচিত ছিল, তাই না? আমার মৃতদেহ ছুঁড়ে ফেলার কথা ছিল শহরের কোনো অজ্ঞাত কোনে। কয়েক দিন পর মর্গে যা শনাক্ত করার কথা ছিল তোমার। সঙ্গে এটাও জানতে পারতে যে হত্যার আগে আমাকে ধর্ষণও করা হয়েছিল। হত্যাকারীরা অবশ্যই ধরা পড়ত না, কারণ আমাদের না আছে অর্থ, না ক্ষমতা। তারপর বাকি জীবনটা সীমাহীন শোক ও অসহ্য লজ্জায় কাটিয়ে কয়েক বছর পর তোমারও মৃত্যু হত। এটাই যে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সে রাতের আকস্মিক আঘাত সবকিছু ওলটপালট করে দিল। শহরের কোনো গলি নয়, আমায় শরীরটা প্রথমে ছুঁড়ে ফেলা হল এভিন জেলের নিঃসঙ্গ কুঠুরিতে, আর সেখান থেকে কবরের মতো এই শহরে রায় কারাগারের সেলে। কিন্তু এ নিয়ে অনুযোগ কোরো না মা, এটাই নিয়তির বিধান। আর তুমি তো জানেনা যে মৃত্যুতেই সব শেষ হয়ে যায় না।
মা, তুমিই তো শিখিয়েছ অভিজ্ঞতা লাভ ও শিক্ষা পাওয়ার জন্যই আমাদের জন্ম। তুমি বলেছিলে, প্রত্যেক জন্মে আমাদের কাঁধে এক বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া থাকে। মাঝে মাঝে লড়াই করতে হয়, সে শিক্ষা তো তোমার কাছ থেকেই পেয়েছি। সেই গল্পটা মনে পড়ছে, চাবুকের ঝাঁপটা সহ্য করতে করতে একবার প্রতিবাদ জানানোর ফলে আরও নির্মমতার শিকার হয়েছিল এক ব্যক্তি। শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু প্রতিবাদ তো সে করেছিল। আমি শিখেছি, সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে অধ্যবসায় প্রয়োজন। তার জন্য যদি মৃত্যুও আসে, তাকেই মেনে নিতে হয়। স্কুলে যাওয়ার সময় তুমি শিখিয়েছিলে, নালিশ ও ঝগড়াঝাটির মাঝেও যেন নিজের নারীসত্তাকে বিসর্জন না দিই। তোমার মনে আছে মা, কত যত্ন করেই না মেয়েদের খুঁটিনাটি সহবত শিখিয়েছিলে আমাদের? কিন্তু তুমি ভুল জানতে, মা। এই ঘটনার সময় আমার সেসব তালিম একেবারেই কাজে লাগেনি। আদালতে আমায় এক ঠান্ডা মাথার খুনি হিসাবে পেশ করা হয়। কিন্তু আমি চোখের জল ফেলিনি। ভিক্ষাও করিনি। আমি কাঁদিনি, কারণ আইনের প্রতি আমার অটুট আস্থা ছিল। কিন্তু বিচারে বলা হল, খুনের অভিযোগের মুখেও নাকি আমি নিরুত্তাপ। আচ্ছা মা, আমি তো কোনোদিন একটা মশাও মারিনি। আরশোলাদের চটিপেটা না করে শুড় ধরে জানলার বাইরে ফেলে দিয়েছি। সেই আমিই নাকি মাথা রেখে মানুষ খুন করেছি! উলটে ছোটোবেলার ওই কথাগুলো শুনে বিচারপতি বললেন, আমি নাকি মনে মনে পুরুষালি। তিনি একবার চেয়েও দেখলেন না, ঘটনার সময় আমার হাতের লম্বা নখের উপর কী সুন্দর নেল পালিশের জেল্লা ছিল। হাতের তালু কত নরম তুলতুলে ছিল।
সেই বিচারকের হাত থেকে সুবিচার পাওয়ার আশা অতি বড়ো আশাবাদীও করতে পারে কি? তাই তো নারীত্বের পুরস্কার হিসেবে মাথা মুড়িয়ে ১১ দিনের নির্জনবাসের হুকুম দেওয়া হল। দেখেছ মা, তোমার ছোট্ট রেহানা এই ক-দিনেই কতটা বড়ো হয়ে গিয়েছে?
এবার আমার অন্তিম ইচ্ছেটা বলি, শোনো। কেঁদো না মা, এখন শোকের সময় নয়। ওরা আমায় ফাঁসি দেওয়ার পর আমার চোখ, কিডনি, হৃদযন্ত্র, হাড় আর যা যা কিছু দরকার— যেন আর কারও জীবন রক্ষা করতে কাজে লাগানো হয়। তবে যিনিই এসব পাবেন, কখনোই যেন আমার নাম না জানেন। আমি চাই না, এর জন্য আমার সমাধিতে কেউ ফুলের তোড়া রেখে আসুক, এমনকি তুমিও না। আমি চাই না, আমার কবরের সামনে বসে কালো পোশাক পরে কান্নায় ভেঙে পড়ো তুমি। বরং আমার দুঃখের দিনগুলো সব হাওয়ায় ভাসিয়ে দিও।
এই পৃথিবী আমাদের ভালোবাসেনি, মা। চায়নি, আমি সুখী হই। এবার মৃত্যুর আলিঙ্গনে তার পরিসমাপ্তি ঘটতে চলেছে। তবে সৃষ্টিকর্তার এজলাসে সুবিচার আমি পাবই। সেখানে দাঁড়িয়ে আমি অভিযোগের আঙুল তুলব সেই সমস্ত পুলিশ অফিসারের দিকে, বিচারকদের দিকে, আইনজীবীদের দিকে, আর তাঁদের দিকে যাঁরা আমার অধিকার বুটের নীচে পিষে দিয়েছে বিচারের নামে মিথ্যা ও অজ্ঞানতার কুয়াশায় সত্যকে আড়াল করেছে। একবারও বোঝার চেষ্টা করেনি, চোখের সামনে যা দেখা যায় সেটাই সর্বদা সত্যি নয়।
আমার নরম মনের শোলেহ, মনে রেখো সেই দুনিয়ায় তুমি আর আমি থাকব অভিযোগকারীর আসনে। আর ওরা দাঁড়াবে আসামির কাঠগড়ায়। দেখিই না সৃষ্টিকর্তা কী চান। তবে একটাই আর্জি, মৃত্যুর হাত ধরে দীর্ঘ যাত্রা শুরুর প্রাক মুহূর্ত পর্যন্ত তোমায় জড়িয়ে থাকতে চাই, মাগো, তোমাকে যে খুব খুব ভালোবাসি…।”
তবে রেহানার মৃত্যুদণ্ডের কারণ নিয়ে অন্যেরা অন্য মতও পোষণ করেন। তাঁরা বলছেন— ইরানের রেহানা জাব্বারি নামে এক মহিলার মৃত্যুদণ্ড নিয়ে সারা বিশ্বে ব্যাপক অপপ্রচার চলছে। গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমগুলোতে ঝড় উঠেছে ওই নারীর পক্ষে, তবে নিতান্তই অসত্যের পক্ষে। প্রকৃত সত্য হল রেহানা ধর্ষণ প্রতিরোধ করতে গিয়ে খুন করেননি। ঘটনাটি ভুলভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে। ইরানের বিচার বিভাগ এতটা নারী-বিদ্বেষী নয় যে, অন্যায়ভাবে একজন নারীকে ফাঁসি দেবে। হত্যাকাণ্ডটি পূর্বপরিকল্পিত ছিল। ওই মহিলা তাঁর দোষ স্বীকার করেছেন আদালতে। রেহানা নিজেকে নির্দোষ প্রমাণেও ব্যর্থ হয়েছেন। ঘটনাটি হচ্ছে দুজনের অবৈধ সম্পর্কের জের ধরে এক পর্যায়ে তাঁদের মধ্যে টানাপড়েন সৃষ্টি হয় এবং এই খুনের ঘটনা ঘটে। সে ক্ষেত্রে পুরুষ লোকটি যে ভালোমানুষ ছিলেন তা বলার সুযোগ নেই। টানাপড়েনের একটি পর্যায়ে বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে। যার কারণে রেহানা লোকটিকে খুনের সিদ্ধান্ত নেন। খুনের দুই দিন আগে রেহানা নতুন ছুরি কিনেছিলেন এবং তাঁর এক বান্ধবীকে এসএমএস করেছিলেন যে, খুনের ঘটনাটি ঘটতে যাচ্ছে। এই মহিলার সঙ্গে ইরানের আদালতের এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি যে, তাঁকে ফাঁসি দিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় দিয়ে দেবে। অথবা এই মহিলা ইরানের জন্য কোনো হুমকি ছিলেন সে কারণে তার ফাঁসি কার্যকর করা হল। বরং যদি এমন হত যে, খুন হয়নি বরং অবৈধ সম্পর্ক বা ধর্ষণের ঘটনার বিচার হচ্ছে, তাহলে ওই পুরুষ লোকটাও মৃত্যুদণ্ডের মুখে পড়ত। এবং এ ক্ষেত্রেও ইরানের আইন অনুসরণ করা হত। দেখা হত না কে পুরুষ আর কে নারী। যেমনটি দেখা হয়নি রেহানার ক্ষেত্রে। আলোচ্য হত্যাকাণ্ডটি ২০০৭ সালে সংঘটিত হয়। ঘটনাটি সাত বছর ধরে পুঙ্খানুপঙ্খ বিচার বিশ্লেষণ করে তারপর ইরানের আদালত রায় দিয়েছে। এ নিয়ে উচ্চ আদালতে পরে আবার বিচার হয়েছে এবং রায় বহাল রাখে। তারপরও এক মাস দেরি করা হয়েছে যে ভিক্টিম পরিবার যদি মাফ করে দেয় তাহলে ফাঁসিটি কার্যকর করা হবে না। কিন্তু ওই পরিবার মাফ করেনি। ইরানের বিচারব্যবস্থায় খুনের ঘটনায় কারও মৃত্যুদণ্ড হলে ভিক্টিম পরিবার ছাড়া কারও পক্ষে সে রায় উল্টানোর সুযোগ নেই। এমনকি প্রেসিডেন্ট বা সর্বোচ্চ নেতাও পারেন না।
কোনোভাবেই মৃত্যুদণ্ড সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। হত্যা করার অধিকার কারোর থাকতে পারে না। নখের বদলে নখ, দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ– এ ব্যবস্থা সমাজে কোনো কাজে লাগে না। এটা প্রতিহিংসাপরায়ণতা। অপরাধের বদলে অপরাধ করা।
সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে ভিন্নমত প্রকাশ লেখকদের জন্য সবসময় ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। আছে এবং হয়তো-বা থাকবে। ভিন্ন মতাবলম্বী লেখকের উপর যে-কোনো সময়ে রাষ্ট্রের খড়গহস্ত নেমে আসতে পারে। গ্রেফতার হতে পারেন লেখক, লেখক নির্বাসিত হতে পারেন, এবং মৃত্যুদণ্ড পেতে পারেন। শুধু রাষ্ট্রই নয় –বিভিন্ন ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর সংঘবদ্ধ আক্রমণের শিকার হতে পারে লেখক। সেই লেখক যদি সরকারের অপ্রিয়ভাজন হন তাহলে রাষ্ট্র সেই সুযোগ নিয়ে সেই একই পদ্ধতি প্রয়োগ। হতে পারে।
ধর্ম এবং বিজ্ঞান বিষয়ে নতুন চিন্তাধারা প্রকাশ করেছিলেন ইটালিয়ান দার্শনিক ও বিজ্ঞানী জিওর্ডানো ব্রুনো তাঁর রচনাসমূহে। সাত বছর বাপী মামলার পরে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে আগুনে পুড়িয়ে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে আয়ারল্যান্ডের কবি ও শিক্ষক প্যাট্রিক হেনরি পিয়ার্স তাঁর সহবিপ্লবীদের নিয়ে ব্রিটিশদের ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি ধরা পড়েন এবং তাঁকে ফায়ারিং স্কোয়াডের গুলিতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। স্পেনের সুবিখ্যাত লেখক ও নাট্যকার ফেডারিকো গার্সিয়া লোরকাকে স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধের প্রথমদিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল ন্যাশনালিস্ট সিভিল গভর্নর। জেনারেল ফ্রাঙ্কোর সেনাবাহিনী তাঁকে প্রথমে অকথ্য অত্যাচার করে এবং পরে তাঁকে হত্যা করা হয়। তাঁর কবর খুঁজে পর্যন্ত যায়নি।
সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম বিষয়ে এখন মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক বদলে গিয়েছে। এমনকি যাঁরা ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি তাঁদের মধ্যেও নিজেদের ধর্ম বিষয়ে নতুন চিন্তাভাবনা এসেছে। এর কারণ হচ্ছে মানুষ চেয়েছে ধর্মের আওতায় থেকেও পরিবর্তিত যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে। আর তার ফলে মৃত্যুদণ্ডসহ বিভিন্ন ইসুতে ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি বদলে গিয়েছে।
বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ‘পঞ্চশিলা’-তে বলা হয়েছে –“প্রত্যেকেই শাস্তিকে ভয় পায়। প্রত্যেকেই মৃত্যুকে ভয় পায়। ঠিক তোমারই মতো। সুতরাং তুমি কাউকে হত্যা করবে না, অথবা এমন কিছু করবে না যার ফলে কেউ নিহত হতে পারে।” বলা হয়েছে –“তাকেই আমি ব্রাহ্মণ বলব যে অস্ত্র ছেড়ে দিয়েছে এবং সকল প্রাণীর বিরুদ্ধে সহিংসতা ছেড়ে দিয়েছে। সে কাউকে হত্যা করে না। সে অন্য কোনো ব্যক্তিকে হত্যায় সাহায্য করে না। অনেক বৌদ্ধগণ মনে করেন কোনো আইনগত পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার বিরোধী তাঁদের ধর্ম। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশগুলোর মধ্যে বেশির ভাগ দেশে কিছু অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ৮১৮ খ্রিস্টাব্দে জাপানের সম্রাট সাগা মৃত্যুদণ্ড বন্ধ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও কিছু জমিদার তাদের এলাকায় মৃত্যুদণ্ড চালু রেখেছিলেন। ১১৬৫ খ্রিস্টাব্দে জাপানে আবার মৃত্যুদণ্ড চালু হয়। এখনো তাই। অবশ্য সম্প্রতি জাপানের কিছু বিচারক মৃত্যুদণ্ড সই করতে রাজি হননি। এ ক্ষেত্রে যুক্তিস্বরূপ তাঁরা নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য বৌদ্ধপ্রধান দেশগুলোর মধ্যে ভুটান ও মঙ্গোলিয়া মৃত্যুদণ্ড নিষিদ্ধ করেছে। শ্রীলংকা একসময়ে মৃত্যুদণ্ড বন্ধ করলেও আবার সেটা চালু করেছে। থাইল্যান্ডে মৃত্যুদণ্ড বরাবরই চালু ছিল এবং আছে। তবে থাইল্যান্ডের বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারকদের মধ্যে এ বিষয়ে মতভিন্নতা আছে। বুদ্ধ তার বাণী দিয়ে খুনি এবং অপরাধীদের যে সংশোধিত করেছিলেন সে বিষয়ে বৌদ্ধ পুরাণে অনেক কাহিনি আছে। যেমন, আঙ্গুলিশালা ৯৯৯ জনকে হত্যার পর নিজের মা এবং বুদ্ধকে হত্যার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বুদ্ধের প্রভাবে তিনি অনুতপ্ত হন এবং বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। সব পশুপ্রাণী হত্যা সম্রাট অশোক নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং তিনি চেয়েছিলেন মানুষ হত্যার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে। মৃত্যুদণ্ড বিষয়ে ক্যাথলিক খ্রিস্টান ধর্মে বহু রকমের মতামত আছে। কেউ মনে করেন, জিশু যে ক্ষমার বাণী প্রচার করেছিলেন তার সম্পূর্ণ বিরোধী মৃত্যুদণ্ড, কারণ এটি প্রতিহিংসার বাস্তবায়ন। সুতরাং এটি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। আবার কেউ মনে করেন, ওল্ড টেস্টামেন্ট আইন অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত। মৃত্যুদণ্ড-বিরোধীরা মনে করিয়ে দেন, জিশু বলেছিলেন, এক গালে চড় খেলে আর-এক গাল বাড়িয়ে দিতে। তাঁরা মনে করিয়ে দেন, পরকীয়া প্রেমে অভিযুক্ত ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত এক নারীকে যখন পাথর ছুঁড়ে মারা হচ্ছিল তখন জিশু সেটা বন্ধ করেন। মৃত্যুদণ্ড-বিরোধীরা বলেন, এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয়, শারীরিকভাবে প্রতিশোধ নেওয়ার বিপক্ষে ছিলেন যিশু। কিন্তু মৃত্যুদণ্ডের পক্ষেও ক্যাথলিক খ্রিস্টানরা আছেন। আমেরিকায় সকল ধরনের মৃত্যুদণ্ডের বিরোধিতা যাঁরা সবচেয়ে আগে করেছিলেন তাদের মধ্যে ছিলেন প্রটেস্টান্ট খ্রিস্টানদের একটি শাখা, দি রিলিজিয়াস সোসাইটি অফ ফ্রেন্ডস বা কোয়েকার চার্চ। সাদার্ন ব্যাপটিস্টরা খুন ও দেশদ্রোহিতার দায়ে দণ্ডিতদের মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করলেও তারা বলেন, সেখানে যেন কোনো ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা অথবা রাষ্ট্রীয় বৈষম্য না থাকে। ইউনাইটেড মেথডিস্ট চার্চ এবং অন্যান্য মেথডিস্ট চার্চও মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী। তাঁরা বলেন, সামাজিক প্রতিশোধ নিতে কোনো মানুষকে মেরে ফেলা উচিত নয়। মেথডিস্ট চার্চ আরও বলে, মৃত্যুদণ্ডের শিকার হয় অসমভাবে গরিব, অশিক্ষিত, সংখ্যালঘু এবং মানসিক রোগাক্রান্ত অথবা আবেগপ্রবণ মানুষরা। হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থে মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে এবং বিপক্ষে বলা হয়েছে। হিন্দু ধর্মে অহিংসার বাণী প্রচারিত হয়েছে যেখানে দাবি করা হয়েছে “আত্মা অবিনশ্বর … মৃত্যু কেবল দৈহিকভাবে হতে পারে।” কিন্তু ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে, খুনের কারণে এবং ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধের সময়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যেতে পারে। মৃত্যুদণ্ড বিষয়ে ইসলামী জ্ঞানীজনদের মধ্যে কিছু বিতর্ক আছে। প্রায় সব ইসলামি দেশে মৃত্যুদণ্ডের বিধান আছে। তবে সেটা কার্যকরের পন্থা হয় ভিন্ন। কিছু ইসলামী দেশে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে বাঁচতে পারেন। বর্তমান যুগে অধিকাংশ খ্রিস্টানরা যেমন মৃত্যুদণ্ডের বিরোধী অবস্থান নিয়েছেন তেমনটা মুসলিমরা করেননি। তদুপরি কিছু মুসলিম দেশে প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করায় এবং সেই ছবি পত্রিকা ও ইন্টারনেটে প্রকাশ করায় মুসলিমরা সাধারণত চিত্রিত হয়েছেন মৃত্যুদণ্ডের পক্ষপাতী এবং প্রাচীনপন্থী রূপে। ইহুদি ধর্মে নীতিগতভাবে মৃত্যুদণ্ডকে সমর্থন করা হয়। তবে সেই দণ্ড দেওয়ার আগে সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থা ও প্রয়োজনীয় সকল সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একটি নির্দেশে বলা হয়েছে, মৃত্যুদণ্ডের মামলায় তিনজন নয়, অন্ততপক্ষে ২৩ জন বিচারককে থাকতে হবে। দ্বাদশ শতাব্দীর ইহুদি জ্ঞানী ব্যক্তি মুসা ইবনে মায়মুন বলেন, একজন নিরপরাধের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার চাইতে এক হাজার অপরাধীকে ছেড়ে দেওয়া শ্রেয়। মুসা বিন মায়মুন যুক্তি দেন, সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত না হয়ে একজন অভিযুক্তকে মেরে ফেললে আমরা একটা পিচ্ছিল পথে পড়ে যাব এবং শেষপর্যন্ত বিচারকের অভিরুচি মোতাবেক দণ্ড হবে। “It is better and more satisfactory to acquit a thousand guilty persons than to put a single innocent one to death… that executing a defendant on anything less than absolute certainly would lead to a slippery slope of decreasing burdens of proof, until we would be convicting merely, according to the judge’s caprice.”
কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর মনে করেন, সন্ত্রাসবাদীদেরও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া উচিত নয়। শশী থারুর ট্যুইট করে বললেন, “এটি একটি বিলুপ্তপ্রায় শাস্তি। এইসব দোষীদের কোনও ছুটি না-দিয়ে সারাজীবন জেল বন্দি করে রাখা উচিত।” শশী বলেন, “একসময় সমাজে এই ধারণা ছিল যে কেউ কাউকে খুন করলে তাকে মৃত্যুর সাজাই দিতে হবে। আমরা এযুগে দাঁড়িয়ে কেন সেই পন্থা অবলম্বন করব? আমরা যখনই মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করি, তখন আমরা ওদের জায়গাতেই পৌঁছে যাই। ওরা খুনি। তাই বলে আমাদের উচিত নয় ওদের মতো ব্যবহার করা।” মুম্বই বিস্ফোরণে দোষী সাব্যস্ত ইয়াকুব মেমনের ফাঁসির পর দুঃখপ্রকাশ করে টুইট করেছিলেন শশী থারুর। সেই প্রসঙ্গে এদিন এই কংগ্রেস সাংসদ বলেন, “আমি কোনও নির্দিষ্ট মামলার বিরুদ্ধে একথা বলিনি। মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির বিরুদ্ধে বলেছি।” থারুর জানান, ইতিমধ্যেই ১৪৩টি দেশে মৃত্যুদণ্ড উঠে গিয়েছে। অন্য ২৫ টি দেশে আইনে থাকলেও তা প্রয়োগ করা হয় না। মাত্র ৩৫ টি দেশে এই আইনের প্রয়োগ রয়েছে।
অপরাধবিজ্ঞানী ও সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিতরা মনে করেন, সুসংগঠিত সুস্থিত সমাজব্যবস্থায় কিছু সংখ্যক মানুষ কেন অসুস্থ-অস্বাভাবিক-অসামাজিক মানসিকতায় সমাজবিরোধী অপরাধে প্রবৃত্ত হয় এবং কঠোর শাস্তির বিধান ও দৃষ্টান্ত থাকলেও কেন অপরাধ থেকে নিবৃত্ত হয় না? মানুষের সামাজিক অস্তিত্বে আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় চিন্তাভাবনা এবং নানান মানসিক ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া কার্যকর থাকে। এসব বিষয়ে সমাজবিজ্ঞান ও অপরাধবিজ্ঞানে গবেষণা চলছে। আর্থ-সামাজিক প্রভাব, অপরাধমনস্কতা, বংশানুক্রমিক বা জিনগত প্রবণতা– মানসিক ও শারীরিক প্রক্রিয়ার দ্বারা অপরাধীর সংশোধন প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে জড়িত। প্রাচীন ভারতে এবং অন্যান্য দেশেও সমাজতাত্ত্বিক ও দার্শনিক আদর্শে মানুষ নামক প্রাণীটির সম্পর্কে দু-রকম ভাবনা নিবদ্ধ। মনু দণ্ডের আলোচনায় বলেছেন– দণ্ড ছাড়া সমাজ অচল। কারণ সবদিক বিচারে একেবারে খাঁটি মানুষ বিরল। “দুর্লভো হি শুচির নরঃ”।
মানুষ জৈবিক কারণে (ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও যৌনতাড়নায়) এবং সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিতাড়িত হয়ে অনেকসময় অপরাধে প্ররোচিত হয়। অর্থাৎ সামাজিক বৈষম্য এবং বিরুদ্ধ অবস্থায় অসহিষ্ণু হয়ে মানুষ অপরাধে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং তাঁদের মতে অপরাধ তথা অপরাধী দুই-ই সমাজের সৃষ্টি। অতএব মৃত্যুদণ্ড দিয়ে হত্যার পথ থেকে সরে গিয়ে সমাজব্যবস্থাকে সার্বজনীন কল্যাণ এবং সুসংহত আদর্শের অনুকূল করে গড়ে তুলতে পারলে সমাজ থেকে অনেক অপরাধই লুপ্ত হয়ে যাব। চাই একটা সাম্যের সমাজ। সাম্যের সমাজ তৈরি করতে পারলে অপরাধমুক্ত পৃথিবী উপহার দেওয়া সম্ভব।
পজিটিভিস্ট স্কুল, যেমন –Lombroso, Ferri, Goring অপরাধীদের আচার ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করেছেন। তাঁদের মতে, প্রত্যেকটি কার্যের কারণ আছে। সমাজ-পরিবেশ মানুষের অপরাধ প্রবণতা বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং অপরাধ না করার ইচ্ছাশক্তিকে দূবল করে দিতে পারে। সেইজন্যে অপরাধের সমস্ত দায় স্বাধীন ইচ্ছার অজুহাতে অপরাধীর কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া যথার্থ নয়। রাষ্ট্রকেই সেই অপরাধের নৈতিক দায়িত্ব নিতে হবে। অতএব অপরাধীর শিরচ্ছেদ করে নয়, মানবিক ব্যবহার করতে হবে।
“crime was read for the first time not as the wickedness of individuals but as an indictment society”– সুতরাং সমাজ just নয়, প্রতিষ্ঠানগুলোও ‘unjust’। আমেরিকার অন্যতম মৃত্যুদণ্ডপন্থী Ernest Vanden Haag বলেছেন, প্রয়োগে মৃত্যুদণ্ড বৈষম্যমূলক হতে পারে, অন্যায্য হতে পারে এবং তা হতে যে-কোনো শাস্তির ক্ষেত্রেই। তাই তার দ্বারা নীতিগতভাবে মৃত্যুদণ্ড বাতিল করার প্রশ্নটি যুক্ত করা ঠিক নয়। প্রয়োগ ও তত্ত্বের বিভাজন করা প্রয়োজন। Haag স্বীকার করে নিচ্ছেন, মৃত্যুদণ্ডের বৈষম্যমূলক প্রয়োগ হয় এবং যা অন্যায় ও অন্যায্য।
ডেভিড আব্রাহামসেন অপরাধ ও অপরাধী প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন– একটি অপরাধ কর্ম অনেকগুলো কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত শর্তের উপর নির্ভর করে। যেমন যদি আমরা অপরাধ কর্মকে ধরি ‘c’, তাহলে সেই কাজের দুটি উপাদার কাজ করে– (১) ব্যক্তির অপরাধ প্রবণতা ঝোঁক (T) এবং (২) সমাজের আর্থ-সামাজিক অবস্থা (S)। এই দুইকে আবার যদি ব্যক্তির প্রতিরোধ ক্ষমতা (R) দিয়ে ভাগ করা যায় তাহলে অপরাধ কর্মটি বোঝা যাবে। অর্থাৎ
C= (T+S)/R
যেটা দাঁড়াল, সেটা হল অপরাধী অপরাধ করতে উদ্যত হয়, যখন সে আর্থ সামাজিক পরিবেশের নানা চাপ কতটা সহ্য করতে পারছে বা পারছে না, তার উপর নির্ভর করে।
কিছুদিন আগে ভারতে এক সন্ত্রাসবাদীর মৃত্যুদণ্ডকে কেন্দ্র করে জনৈক ব্যক্তি ফেসবুকে একটি পোস্ট দিয়ে বললেন, যাঁরা মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখছেন তাঁরা আসলে দেশদ্রোহী। তিনি আরও বলেছিলেন, এদের মৃত্যুদণ্ড না দিয়ে আমৃত্যু সশ্রম কারাদণ্ড দিলে আমাদের ট্যাক্সের টাকা থেকে পুষতে হবে কেন? আমি বলি— ট্যাক্সের টাকা? কী হয় আমাদের ট্যাক্সের টাকা দিয়ে? কোথায় খরচ হয়ে যায় সেই টাকা? সুইস ব্যাঙ্কে যে হাজার হাজার কোটি কালো টাকা যেসব মহামতিরা গচ্ছিত রেখেছেন তারা কি দেশপ্রেমী? এই যে হাজার হাজার কোটি টাকা তাঁদের সুইস ব্যাংকে গচ্ছিত আছে সেগুলি কোন্ টাকা? দেখবেন নাকি পাসবইগুলি? এইসব তথ্য WikiLeaks-এ ফাঁস হয়েছে। (১) Ashok Gehlot (২,২০,০০০ কোটি টাকা), (২) Rahul Gandhi (১,৫৪,০০০ কোটি টাকা), (৩) Harshad Mehta (১,৩৫,৮০০ কোটি টাকা), (৪) sharad Pawar (৮২,০০০ কোটি টাকা), (৫) Ashok Chavan (৭৬,৮৮৮ কোটি টাকা), (৬) Harish Rawat (৭৫,০০০ কোটি টাকা), (৭) Sonia Gandhi (৫৬,৮০০ কোটি টাকা), (৮) Muthuvel_Karunanidhi (৩৫,০০০ কোটি টাকা), (৯) Digvijay Singh (২৮,৯০০ কোটি টাকা), (১০) Kapil sibal (২৮,০০০ কোটি টাকা), (১১) Rajeev Gandhi (১৯,৮০০ কোটি টাকা), (১২) Palaniappan Chidambaram (১৫,০৪০ কোটি টাকা), (১৩) Jayaram Jaylalitha (১৫,০০০ কোটি টাকা), (১৪) Kalanithi Maran (১৫,০০০ কোটি টাকা), (১৫) HD Kumarswamy (১৪,৫০০ কোটি টাকা), (১৬) Ahmed Patel (৯০০০ কোটি টাকা), (১৭) JM Scindia (৯০০০ কোটি টাকা), (১৮) Ketan Parekh (৮,২০০কোটি টাকা), (১৯) Andimuthu Raja (৭,৮০০ কোটি টাকা), (২০) Suresh_Kalmadi (৫,৯০০ কোটি টাকা)।
(http://www.india.com/news/india/list-of-black-money holders-in-swiss-bank-accounts-leaked-by-wikileaks-182160/)
এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ভারতের কোনো কাজে লাগবে? এত হাজার হাজার কোটি টাকা সব দেশ থেকে বিদেশে চলে গেল!! দেশ সর্বস্বান্ত হল। লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি আর মুদ্রাস্ফীতির জন্য কে বা কারা দায়ী? আর একটা মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত মানুষকে বাঁচিয়ে রেখে সশ্রম কারাদণ্ড দিলে কত কোটি টাকা খরচা হয়ে যেত? জেলে আসামীদের রেখে দিলে যদি আপনার ট্যাক্সের টাকা খরচা হয়ে যায়, তাহলে তো লাখো লাখো জেলবন্দি সাজাপ্রাপ্ত আসামীদের হত্যা করে ফেলা উচিত। শুধু যে সাজাপ্রাপ্ত আসামীরাই জেলবন্দি থাকে তা তো নয়, বহু অভিযুক্ত বিনা বিচারে জেলখানাগুলিতে বছর বছর ধরে পচছে। টাকা লাগে না? টাকা লাগে বলে মৃত্যুদণ্ড বা হত্যা করা কোন যুক্তিতে? প্রাণদণ্ড বহাল রাখা মানবাধিকারের পরিপন্থী। এই দণ্ড বিচারক ও জুরি মহোদয়দের ব্যক্তিগত নীতিবোধ, আবেগ-অনুভূতি, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, জন্মগত সংস্কার-পরম্পরা এবং পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী প্রযুক্ত হয়। কখনো-কখনো তাঁদের ভুল সিদ্ধান্তের ফলে নির্দোষ মানুষও এমন দণ্ড পায়। কোনো-কোনো ক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ সাপেক্ষে এই দণ্ড বিহিত হয়। পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে খুব কম খুনিই দ্বিতীয়বার খুন করে। কিন্তু ফাঁসুড়েরা একাধিকবার খুন করে। খুন করে রাষ্ট্রের নির্দেশে। অনেকেক্ষেত্রেই এইসব ফাঁসুড়েরা হয় সাজাপ্রাপ্ত আসামীরা। প্রাসঙ্গিক কারণেই, আমি এমনই এক ফাঁসুড়ের কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই, যিনি নিজেই একজন সাজাপ্রাপ্ত আসামী। বঙ্গবন্ধুর খুনী এবং মানবতাবিরোধী অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত কাদের মোল্লার ফাঁসি কার্যকরের পর যে কয়েকটা নাম খুব বেশি আলোচিত হয়েছে তার মধ্যে একটি নাম শাহজাহান। শাহজাহানের পুরো নাম কাদের মোহম্মদ শাহজাহান ভূঁইয়া। জেলখানার ভিতর তাকে ‘জল্লাদ শাহজাহান’ নামেই চেনেন সবাই। এই শাহজাহান জেলখানার ভিতরে কাটিয়ে দিয়েছেন জীবনের অনেকগুলি বসন্ত। জল্লাদ শাহজাহান দীর্ঘ ৩৬ বছর যাবৎ কারাবন্দি অবস্থার আছেন। রাষ্ট্রের নির্দেশে এ পর্যন্ত ৪৫ জনকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করেছেন তিনি। ব্যক্তি হিসেবে শাহজাহান ভূঁইয়া খুবই ভালো প্রকৃতির ছিলেন। পারতপক্ষে কারোর উপকার ছাড়া ক্ষতি করার চেষ্টা করতেন না। তিনি প্রচণ্ড বন্ধুপাগল ছিলেন। একবার তার গ্রামে নারীঘটিত একটি ঘটনা ঘটে। তাতে দুই বন্ধুসহ তার নামে অভিযোগ ওঠে। তাকে নিয়ে গ্রামে বিচার সালিশ বসে। সেই বিচারে তাকে অপরাধী প্রমাণ করে সাজা দেওয়া হয়। এরপর থেকেই তার ক্ষিপ্রতা শুরু। তিনি অপমান সহ্য করতে না-পেরে সিদ্ধান্ত নেন অপরাধ জগতে প্রবেশ করে এই অপমানের চরম প্রতিশোধ নেবেন। নারীঘটিত ওই ঘটনার পর শাহজাহান ভূঁইয়া বাংলাদেশের একজন বহুল পরিচিত সন্ত্রাসীর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। তা ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করার পর থেকে যে-কোনো অপারেশনে তার চাহিদা দিন দিন বাড়তে থাকে। তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অপারেশন করেছিলেন ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে মাদারিপুর জেলায়। আর তা ছিল শাহজাহান ভূঁইয়ার জীবনের শেষ অপারেশন।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ জানতে পারে শাহজাহানের দল মানিকগঞ্জ হয়ে ঢাকায় যাবে। রাতভর মানিকগঞ্জে পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধ হলেও পুলিশ তাকে ধরতে পারেনি। শাহজাহান ঢাকায় পৌঁছে যখন নরসিংদীর উদ্দেশে রওনা হন। পথে পুলিশ তাকে আটক করে এবং তার গতিময় জীবনের সমাপ্তি ঘটে। শুরু হয় বন্দিজীবন। ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দে আটক হওয়ার আগে ও পরে তার নামে সর্বমোট ৩৬টি মামলা হয়। এর মধ্যে একটি অস্ত্র মামলা, একটি ডাকাতি মামলা এবং ৩৪টি হত্যা মামলা। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে তার যাবজ্জীবন সাজা হয়। এরপর ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে তার ১৪৩ বছরের সাজা হয়। পরে উচ্চ আদালতের নির্দেশে ১০০ বছর মকুব হয়ে ৪৩ বছরের জেল হয়। জেল থেকে বের হওয়ার তারিখ শাহজাহানের জেল কার্ডের উপর লেখা আছে ‘ডেট অব রিলিজ ২০৩৫’।
যখন তিনি কারাগার থেকে মুক্তি পাবেন তখন তার বয়স হবে ৮৫ বছর। কী লাভ হবে তখন কারাগার থেকে বের হয়ে? এ জন্য তিনি সিদ্ধান্ত নেন জল্লাদের খাতায় নাম লেখাতে। তিনি জানতেন একটা ফাঁসি দিলে দুই মাস চার দিনের সাজা কমে। এভাবে যদি সাজা কিছুটা কমে! জেলারের অনুমতি নিয়ে ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দে প্রথম তিনি সহযোগী জল্লাদ হিসাবে গফরগাঁওয়ে নুরুল ইসলামকে ফাঁসি দেন। ওটাই ছিল শাহজাহানের জীবনে কারাগারে কাউকে প্রথম ফাঁসি দেওয়া। তাঁর যোগ্যতা দেখে আট বছর পর ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে কারা কর্তৃপক্ষ তাঁকে প্রধান জল্লাদের আসন প্রদান করে। আর প্রধান জল্লাদ হওয়ার পর ডেইজি হত্যা মামলার আসামি হাসানকে প্রথম ফাঁসি দেন তিনি। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের পর এখন পর্যন্ত সাড়ে চার শতাধিক মানুষকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এক হাজারের বেশি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত কয়েদি কারাগারে রয়েছেন। এর মধ্যে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রয়েছেন শতাধিক। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার ছাড়াও দেশের আরও ১৪টি কারাগারে ফাঁসির মঞ্চ আছে।
জল্লাদ শাহজাহান বলেন, “যারা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছিল তিনি তাঁদের ফাঁসি দিয়েছেন।” তিনি আশা করেছিলেন “শেখের মেয়ে প্রধানমন্ত্রী, সে তাঁর দিকে একটু সুনজর দেবেন। কিন্তু কে রাখে কার খবর? তাঁর কথা কেউ বিবেচনা করেনি।” তিনি বলেন, “নেলসন ম্যান্ডেলা বেশি সময় জেলখানায় কাটিয়ে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছিলেন। আর এখন তিনি (শাহজাহান) জীবনের ৩৬টি বছর কারাগারে কাটিয়ে দিলেন। বাইরে মানুষ হত্যা করলে জেল হয়, ফাঁসি হয়। আর এখানে এত মানুষ হত্যা করছি, কিন্তু কিছুই হয় না।”
মেরঠের কাল্লু ও তাঁর ছেলে মামু এবং পশ্চিমবঙ্গের নাটা মল্লিক মারা যাওয়ার পরে বর্ষীয়ান বাবুই আপাতত ভারতের তথা দেশের একমাত্র ফাঁসুড়ে। ইন্দিরা গান্ধির হত্যাকারী সতবন্ত সিংহ ও কেহর সিংহের ফাঁসিও দিয়েছিলেন বাবু ও কাল্প। নাটা মল্লিক শেষবার ২০০৪ সালে ধনঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়কে ফাঁসি দেন। তবে বাবু অসমে ফের ফাঁসি দিতে আসতে রাজি হলেও বাবুর দুই ছেলে বাবার সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ। তাঁরা ফাঁসুড়ের বৃত্তি গ্রহণে রাজি নন।
যেসব রাষ্ট্র হত্যা করবেনই ঠিক করে ফেলেছেন তখন সাধারণ মানুষকে দিয়ে কেন হত্যা করানো হবে, সেই ব্যক্তি যিনি সাজাপ্রাপ্ত? এই হত্যাকাণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনেতা অথবা প্রধানমন্ত্রী অথবা রাষ্ট্রপতি অথবা দণ্ডদাতা বিচারপতিই কার্যকর করুন না, নিজের হাতে।
এখন প্রশ্ন হল অপরাধের জন্য অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড দিলেই কী আক্রান্ত পরিবারের মানসিক শান্তি মেলে? তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়? ঠিক কোন্ ধরনের শান্তিতে আক্রান্ত পরিবার শান্তি পায়, তা পরিমাপ করা কঠিন। তবে এটা দেখা যায় সবরকমের অপরাধেই ভিকটিম অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চায়, অর্থাৎ ফাঁসি। যে-কোনো অপরাধের যে শাস্তিই প্রদান করা হোক না কেন, তা নানা স্তরে বিচারের মাধ্যমে সাক্ষ্য-সাবুদের তুল্যমূল্য বিচারের পর বিচারপতে শাস্তির রায় দেন। সেই রায় মৃত্যুদণ্ডের মতো রায়ও হতে পারে। অর্থাৎ একটা কলমের খোঁচাতেই ব্যক্তির জীবনের শেষ ঘণ্টা বাজিয়ে দিতে সক্ষম আদালত। সত্যিই কি সবক্ষেত্রে তুল্যমূল্য বিচার হয়? অভিযোগকারী ও অভিযুক্তের প্রভাব ও আর্থিক সক্ষমতা কি বিচারের রায় বদলে দেয় না। একপক্ষ অতি দরিদ্র ও এক ধনী হলে কি অতি দরিদ্রের পক্ষে কি সুবিচার পাওয়া সম্ভব? আইনি লড়াই তো বিনামূল্যে হয় না। একটা দক্ষ আইনজীবী নিয়োগ করতে হলে যে আর্থিক সক্ষমতার প্রয়োজন, তা কি একজন দরিদ্র বিচারপ্রার্থীকে সুবিচার থেকে বঞ্চিত করে না? এমন তো অনেক সময়েই দেখা যায় নিম্ন আদালতের রায় উচ্চ আদালতে গিয়ে বদলে যায়। উচ্চ আদালতের রায় সুপ্রিমকোর্টে খুব কম বদলায়। সুপ্রিমকোর্ট বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উচ্চ আদালতের রায় বহাল রাখে। তবে নিম্ন আদালতের রায় উচ্চ আদালতে গিয়ে বদলে যাওয়ার ঘটনা মোটেই বিরল নয়। একটি মামলার কথা মনে পড়ছে। একটি নিম্ন আদালত মৃত্যুদণ্ডের রায় দিয়েছিল। উচ্চ আদালতে মামলাটি গেলে জানানো হল এই মামলাটি যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ। মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার মতো কোনো উপাদান নেই। এখান থেকেই ভাবতে হবে বিষয়টা। সেই অভিযুক্ত যদি উচ্চ আদালতে না যেতেন বা না যেতে সক্ষম হতেন, তাহলে তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়ে যেত। যদিও নিয়ম অনুসারে নিম্ন আদালত কাউকে মৃত্যুদণ্ড দিলে ওই দণ্ড কার্যকর করতে হলে উচ্চ আদালতের অনুমোদন (ডেথ রেফারেন্স) নিতে হয়। নিয়ম অনুযায়ী এই অনুমোদনের জন্য মামলাটি উচ্চ আদালতে আসে। যাই হোক আমাদের সেই বিচার ব্যবস্থা কি ভুল-ত্রুটি বিচ্যুতিমুক্ত? প্রশ্নাতীতভাবে উত্তর হবে– না। কখনোই তা সম্ভব নয়। তাহলে নির্দোষ ব্যক্তির ফাঁসি হয়ে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থেকে যায়। মৃত্যুদণ্ড এমন একটি শাস্তি, যা অন্যান্য শাস্তি থেকে পৃথক। কী গুণগতভাবে, কী মৌলিকগতভাবে। জীবন নিলে আর সেই জীবন ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। ভুল হলে ভুলের সেই মাশুল শোধ হবে কোন্ উপায়ে? আমরা দেখেছি বহু অভিযুক্ত ১০ বছর ২০ বছর জেল খাটার পর নিরপরাধ প্রমাণ হয়ে মুক্তি পায়। মৃত্যুদণ্ডের ক্ষেত্রে তো সম্ভব নয়।
ভারতের সুপ্রিমকোর্ট কেহার সিং মামলার একটি রায়ে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছিলেন– “falliability of human judgment (is) undeniable even in the most trained mind, a mind resourced by a harvest of experience.” ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার সুপ্রিমকোর্টও একইভাবে বলেছিল– “In its finality the death penalty may cruelly frustrate justice. Death is the one punishment from which there can be no relief in light of later development in the law or the evidence.”
একটি প্রবন্ধে সাংসদ মুকুন্দলাল আগরওয়াল বহু নজির সহ দেখিয়েছিলেন কীভাবে ভুল তথ্য বা সাক্ষ্য-প্রমাণের বিশ্লেষণের জন্য কত মানুষের ফাঁসি হয়েছে। (Capital punishment abolition move_in_India– Mukundlal Agrawal) আইনজীবী কে. জি. সুব্রহ্মমণিয়ম দেখিয়েছেন– বিচারের একটি মানদণ্ডে মাদ্রাজ হাইকোর্টের ফুল বেঞ্চ ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে আত্থাপ্পা গৌদমকে প্রাণদণ্ড দেয়। দরিদ্র হওয়ার কারণে সে তাঁর পরিবার প্রিভি কাউন্সিলে যেতে পারেননি আপিলের জন্য। তাঁর ফাঁসি কার্যকর হয়ে যায়। প্রায় ১০ বছর বাদে অন্য একটি সমধর্মীয় মামলায় প্রিভি কাউন্সিলে বিষয়টি বিশ্লেষিত হয় ও ফাঁসি দেওয়া ভুল হয়েছিল– একথা বলা হয়। গ্রেট ব্রিটেনে টিমোনি জন ইভান্সকে ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে ফাঁসি দেওয়া হয়। পরে জানা যায় সে নির্দোষ ছিল। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে ইভান্সকে মরণোত্তর নির্দোষ ঘোষণা করা হয়। খুনের অভিযোগে ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে ডেরেক বেন্টলের ফাঁসি কার্যকর করা হয়। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুলাই আদালত পুনর্বিবেচনা করে বলে বেন্টলের অপরাধী সাব্যস্ত হওয়াটা ছিল ‘unsafe’। নির্দোষ বেন্টলের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ঘটনা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল।
নির্দোষ ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড হয়েছে এমন ঘটনা গোটা বিশ্বের সব দেশেই প্রভূত সংখ্যক হয়েছে। বর্ণবিদ্বেষ ও দারিদ্রতার কারণেও বহু নির্দোষের মৃত্যুদণ্ড হয়ে গেছে। আর-একটি হল জনমতের চাপ, যা মিডিয়াগুলি লাগাতার তৈরি করে। চার্লি এল, ব্ল্যাকের গবেষণায় উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। সেখানে বলা হচ্ছে আমেরিকার ফৌজদারি ন্যায় ব্যবস্থাটাই শুধু ভুলপ্রবণই নয়, নেই কোনো নির্দিষ্ট মান। স্বেচ্ছাচারী ও চূড়ান্তভাবে শ্বেতাঙ্গ-ঘেঁষা এবং কৃষ্ণাঙ্গ-বিদ্বেষী। জর্জিয়াতে ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত গবেষণা করে অধ্যাপক ডেভিড বলডাস জানিয়েছেন– একজন শ্বেতাঙ্গকে হত্যা করা শ্বেতাঙ্গের মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার সম্ভাবনার চেয়ে কৃষ্ণাঙ্গ হত্যাকারী শ্বেতাঙ্গের মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার সম্ভাবনা ৮ গুণ কম। শ্বেতাঙ্গ হত্যাকারী কৃষ্ণাঙ্গের সেখানে মৃত্যুদণ্ড পাওয়ার সম্ভাবনা ৩৩ গুণ বেশি। ভারতের মতো দরিদ্রতম দেশগুলিতে বর্ণ-বৈষম্য কোনো ম্যাটার না করলেও বিচার-বৈষম্য দেখা যায় দরিদ্রদের ক্ষেত্রে। ফৌজদারি মামলা সব ধরনের বৈষম্যের শিকার হয় দরিদ্ররাই– সে অভিযুক্তই হোক বা অভিযোগকারী। আইন আইনের পথে চললেও সেই আইনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত দরিদ্ররা। দারিদ্রতার কারণেই আইনের চোখে সবাই সমান হতে সক্ষম হয় না।
বহুকাল আগে থেকেই চালু থাকলেও বিংশ শতাব্দীতে মৃত্যুদণ্ডের বিপক্ষে ক্রমেই বিভিন্ন দেশে জোরালো যুক্তিতর্ক হচ্ছে। বিশেষত মৃত্যুদণ্ড বিলোপের জন্য বিভিন্ন দেশে প্রভাবশালী কিছু সংগঠন গড়ে ওঠে। যেমন ব্রিটেনে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন ও হিউম্যান রাইটস ওয়াচ ইত্যাদি। যাঁদের প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে পৃথিবী থেকে মৃত্যুদণ্ড বিলোপ করা। দেশে দেশে মৃত্যুদণ্ড বিলোপ হওয়ার অন্যতম একটি কারণ হল নির্দোষের মৃত্যুদণ্ড। ভিক্টর হুগো বহুকাল আগে বলেছিলেন, তাঁর কাছে গিলোটিনের নাম Lesurques, একজনের নাম যিনি নির্দোষ ছিলেন। কিন্তু তাঁকে লিয় মেল মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে গিলোটিনে হত্যা করা হয়। হুগোর বক্তব্যে এটা অনুধাবন করা যায়– একজন নির্দোষকে দোষী ভেবে হত্যা করাটাই মৃত্যুদণ্ড বিলোপের কারণ হিসাবে যথেষ্ট। কারণ একজন নির্দোষ ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করে দেওয়া মোটেই কঠিন কারণ নয়। ১৮৩০ খ্রিস্টাব্দে লাফায়েৎ বলেছিলেন– “Till the infalliability of human judgments shall have been proved to me, I shall demand the abolition of the death penalty.” A. C. Ewing of ‘Second Thoughts in Moral Philosophy’ গ্রন্থে বলেছেন –“নির্দোষকে ফাঁসি দিলে তার প্রভাব সমাজে নানাভাবে পড়ে। প্রথমত, এই ধরনের মৃত্যুদণ্ড সমাজের সুষ্ঠু ন্যায়বিচারের ভিতকে সজোরে নাড়িয়ে দেয়। কারণ শাস্তি তো এমন একটি শরীরের উপরে নির্যাতন, যে অপরাধ করছে বলে সমাজ ও রাষ্ট্র ঠিক করেছে। দ্বিতীয়ত, সবচেয়ে আপত্তির বিষয় এই যে, তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে এই বদনাম চাপিয়ে যে, সে অপরাধী।
অপরদিকে মৃত্যুদণ্ডের পক্ষেও মতামত আসতে থাকে, বিশেষত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে যে সাধারণ যুক্তি দেওয়া হয়, তা হল— এর ফলে অপরাধের সংখ্যা কমে যায়, এটা পুলিশ ও সরকারি উকিলের সহায়ক হয়। মৃত্যুদণ্ডের ভয়ে অপরাধী তাঁর অপরাধ স্বীকার করে বিনিময়ে জীবন রক্ষার ডিল করতে পারে, দণ্ডিত অপরাধী আর কোনোদিনই যে অপরাধের পুনরাবৃত্তি করতে পারবে না সেটা মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করে। শিশু হত্যা, সিরিয়াল খুন এবং নির্যাতনমূলক হত্যার মতো নৃশংস অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ডই হচ্ছে ন্যায়সংগত শাস্তি।
মৃত্যুদণ্ড বিরোধীরা যুক্তি দেন যে, এসব যুক্তির বিপরীতে যাঁরা হত্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সবাই যে হত্যাকারীর মৃত্যুদণ্ড চান, তা নয়। যেমন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির হত্যাকারীকে সোনিয়া গান্ধি মকুব করে দিয়েছিলেন। সাধারণত দেখা যায়, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা ও বিত্তশালীরা বিভিন্নভাবে মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যায়। কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠ ও গরিবরা মৃত্যুদণ্ডের শিকার হয়। মৃত্যুদণ্ড সহিংসতার কালচারকে উৎসাহিত করে। ফলে দেশে সহিংসতা বেড়ে যায়। মৃত্যুদণ্ড মানুষের মৌলিক অধিকার লংঘন করে। কিন্তু দোষী ব্যক্তিকে যদি মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে আজীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়, তাহলে সে তো আর অপরাধ করতে পারছে না। বিরল থেকে বিরলতম’ অপরাধের ক্ষেত্রে যদি অপরাধীকে কঠোরভাবে সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয় আমৃত্যু— তাহলে কেন মৃত্যুদণ্ড? (৩) খুনের শাস্তি আর-একটি ‘খুন’ দিয়ে হতে পারে না। এটাকে কোনোভাবেই ন্যায়বিচার বলা যায় না। প্রতিশোধ বলা যেতে পারে। (৪) সংবিধানের জীবনের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। তার সঙ্গে মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখা মোটেও সংগতিপূর্ণ নয়।
দেখা গেছে, সারা বিশ্বে যত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়, তার ৯০ শতাংশই হয় এশিয়ায়। এমনকি আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে সুদান, ইরান এবং সৌদি আরবে ১৮ বছরের কম বয়সিকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। কী ভয়ংকর! চিনে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ২০১২ খ্রিস্টাব্দে এই সংখ্যা চার হাজারেরও বেশি। প্রাচীন এবং মধ্যযুগে প্রায় সব দেশেই প্রকাশ্যেই ফাঁসি দেওয়ার রীতি থাকলেও বর্তমানে ইরান, সৌদি আরব এবং সোমালিয়া ছাড়া অন্য সব দেশে তা বন্ধ করা হয়েছে।
সক্রেটিসকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন তখনকার আদালত। অভিযোগ– তিনি যুবসমাজকে ধ্বংস করছেন। তাঁর বয়স ছিল তখন ৬৩ বছর। তিনি আরও দীর্ঘ জীবন পেলে পৃথিবী আরও কত কী পেত, সেটা ভাবাই যায় না। মৃত্যুদণ্ডের মাধ্যমে এভাবে কত ক্ষতি হয়ে গেল পৃথিবীর, কে তার হিসাব রাখে? একবিংশ শতাব্দীতে এ ধরনের অপরাধের জন্য আর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় না ঠিকই, কিন্তু অন্যান্য অপরাধের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার হার এখনও অনেক বেশি। মূলত হত্যা, নিজ দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, ধর্ষণ, মাদক পাচার এ ধরনের অপরাধের কারণেই মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়ে থাকে। সামান্য কিছু চুরি করার। কারণেও ইংল্যান্ডের মতো দেশে বছরে শত শত মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হত একসময়। অষ্টম হেনরির সময় ৭২,০০০ চোরকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। নিশ্চয়ই সেদিন আর নেই। মানুষ সভ্য হয়েছে বলে দাবি করে। সভ্য হওয়ার নমুনা হিসাবে পৃথিবীর অনেক দেশেই মৃত্যুদণ্ড বিলুপ্ত হচ্ছে একের পর এক। যেসব দেশে এখনও বন্ধ হয়নি, সেখানেও মৃত্যুদণ্ড বন্ধ করার জন্য আন্দোলন চলছে।
বিশ্বব্যাপী প্রায় ৭০ টি মানবাধিকার সংস্থা সর্বোচ্চ শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ডের বিপক্ষে কাজ করে যাচ্ছে। এর মধ্যে লন্ডন ভিত্তিক মনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল অন্যতম। অ্যামনেস্টির দেওয়া তথ্য মতে –“এখন পর্যন্ত ১৪০টি দেশ মৃত্যুদণ্ড আইনগতভাবে বা প্রথা হিসাবে বাতিল করেছে। যে মাত্র নয়টি দেশ ২০০৯ থেকে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বছর ফাঁসি কার্যকর করেছে তার মধ্যে ভারত, বাংলাদেশ অন্যতম।” প্রতিবছর বিশ্বজুড়ে মৃত্যুদণ্ড এবং কার্যকর বিষয়ে অ্যামনেস্টি বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করে। সম্প্রতি প্রকাশিত এক রিপোর্টে দেখা যায়, শাস্তি হিসাবে বিশ্বে ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের তুলনায় ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেওয়ার সংখ্যা বেড়েছে। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে এই সংখ্যাটি ছিল ২ হাজার ৪৬৬ জন, যা আগের বছরের তুলনায় শতকরা হিসাবে ২৮ ভাগ বেশি। মিশর ও নাইজেরিয়ায় গণবিচারে কয়েক শত মানুষকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ায় এই সংখ্যা বেড়েছে। অ্যামনেস্টি বলছে, চিনে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তার কারণে সেখানকার মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের হিসাব পাওয়া যায় না। চিন এই হিসাব প্রকাশ করে না। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল প্রদত্ত বার্ষিক রিপোর্টের পরিসংখ্যান থেকে যায় যে, ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে সারা বিশ্বে মোট ৪২৭২ জন ফাঁসিতে মৃতর মধ্যে ৩৫০০ জন শুধু চিনের। এই তালিকায় এগিয়ে আছে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলি। রাশিয়া, ইউক্রেন, ইরান, তুর্কমেনিস্তান, আমেরিকা, পাকিস্তান, বাংলাদেশ এবং ভারতের মতো রাষ্ট্রগুলিতে মাত্র ওই এক বছরে শত শত মানুষকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দে গোটা দুনিয়ায় হত্যা করা হয়েছিল ৩২৭০ জনকে। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দের মতো ২০১৪ খ্রিস্টাব্দেও ২২টি দেশেই শুধু মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ২০ বছর আগে সংস্থাটি যখন প্রথম প্রতিবেদন প্রকাশ করে তখন মোট ৪২টি দেশে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।
অ্যামনেস্টির ‘ডিরেক্টর অফ গ্লোবাল ইস্যুজ’ অড্রে গাউঘ্রান বলেন, “মৃত্যুদণ্ড কোনো সুবিচার নয়।” মিশর এবং নাইজেরিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে অ্যামনেস্টি ভীষণ উদ্বিগ্ন। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দে নাইজেরিয়ায় ৬৫৯ জন এবং মিশরে কমপক্ষে ৫০৯ জনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। দু-দেশেই বৃদ্ধির হার উদ্বেগজনক। ২০১৩ খ্রিস্টাব্দে ১৪১ জনকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল নাইজেরীয় সরকার। মিশরে সে বছর ১০০-র মতো লোককে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।
আমি মৃত্যুদণ্ড বিরোধী। আমি মনে করি রত্নাকররা বাল্মীকি হতে পারলে ধনঞ্জয়রাও অন্য কিছু হতে পারত। সেদিন যদি রত্নাকরকে জঘন্য খুনের অপরাধের কারণে ক্ষমা না-করে হত্যা করা হত, “রামায়ণ” কোথায় পেতাম? মহাকবি কোথায় পেতাম? রত্নাকরকে বাঁচিয়ে সমাজের কি খুব ক্ষতি হয়ে গেছে? মৃত্যুদণ্ড কোনো রাষ্ট্রের স্বৈরচারিতারই নামান্তর। না, রাষ্ট্রের এহেন স্বৈরাচারিতা মেনে নেওয়া যায় না। আমি মনে করি, প্রতিটি মানুষের বাঁচার অধিকার আছে। একজন ভুল করে একটা অপরাধ করে ফেললে রাষ্ট্র কেন পরিকল্পিতভাবে একজনের জীবন কেড়ে নেবে? মৃত্যুদণ্ডের বদলে অন্য যে-কোনো শাস্তি তাঁরা পেতে পারে। আমৃত্যু যাবজ্জীবন তো পেতেই পারে? নয় কেন? পরে যদি দেখা যায় দণ্ডপ্রাপ্ত সেই ব্যক্তি সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিল, তাহলে তো তাঁকে মুক্তি দিয়ে স্বাভাবিক জীবন ফিরিয়ে যেতে পারে। হত্যা করে দিলে তো সেটা কখনোই সম্ভব নয়। বস্তুত যাবজ্জীবনেও আপত্তি করি। জেলখানা ব্যাপারটাকেই পছন্দ করি না। জেলখানাগুলি হতে পারে সংশোধনী কেন্দ্র। যতদিন মাথার ভিতর থাকা দুষ্টু কীটগুলি মরে যাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত অপরাধীরা থাকবে ওই কেন্দ্রে। কে যেন একজন বলেছিলেন, “জেলখানার ঘরগুলি হতে পারে এক-একটা ক্লাসরুম, আর জেলখানাগুলো এক-একটা বিশ্ববিদ্যালয়”। কিছুদিন আগে সুইডেনের কিছু জেলখানা বন্ধ করে দিতে হয়েছে। কারণ জেলে মোটেও লোক নেই। অপরাধের সংখ্যা কম, তাই আসামীর সংখ্যাও কম। সমাজটাকে বৈষম্যহীন যত করা যাবে, যত সমতা আনা যাবে মানুষে-মানুষে, অপরাধ তত কমে যাবে। কোনো প্রাণীই বা কোনো মানুষই অপরাধী বা সন্ত্রাসী হয়ে জন্ম নেয় না। একটি শিশুকে যদি সুস্থ সুন্দর শিক্ষিত বৈষম্যহীন পরিবেশ দেওয়া না-হয়, একটি শিশুর গড়ে ওঠার সময় যদি তার মস্তিষ্কে ক্রমাগত আবর্জনা ঢালা হতে থাকে, তবে এই শিশুরাই বড়ো হয়ে অপরাধ আর সন্ত্রাসে নিজেদের জড়িয়ে ফেলে। এ কি ওদের দোষ? নাকি যাঁরা আবর্জনা ঢালে, আবর্জনা ঢালার যে প্রথা যাঁরা চালু রাখছে সমাজে, তাঁদের দোষ! একই সমাজে বাস করে আমি মৌলবাদ-বিরোধী, কেউ মৌলবাদী, কেউ খুনী, ধর্ষক, চোর, আবার কেউ সৎ, সজ্জন। সমাজ এক হলেও শিক্ষা ভিন্ন বলেই এমন হয়। একদল লোক বিজ্ঞান শিক্ষা পাচ্ছে, মানবাধিকার সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করছে, আলোকিত হচ্ছে। আর-এক দলকে ধর্মান্ধ, মূর্খ, কূপমণ্ডুক আর বর্বর বানানো হচ্ছে। ফেলে রাখা হচ্ছে ঘোর অন্ধকারে। শিক্ষার ব্যবস্থাটা সবার জন্য সমান হলে, শিক্ষাটা সুস্থ শিক্ষা হলে, সমানাধিকারের শিক্ষা হলে, মানুষেরা মন্দ না-হয়ে ভালো হত। ছোটখাটো অভদ্রতা, অসভ্যতা, অপরাধ থাকলেও সমাজ এমনভাবে নষ্টদের দখলে চলে যেত না, এত লক্ষ লক্ষ লোক খুনের পিপাসা নিয়ে রাজপথে তাণ্ডব করত না। যে দেশে সবার জন্য খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা স্বাস্থ্য নেই, সেই দেশে অরাজকতা থাকবেই। অন্য সব ব্যবস্থার মতোই বিচারব্যবস্থাতেও আছে পাহাড়প্রমাণ গলদ। বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন, “অপরাধীর যথার্থ দণ্ড না হইলে সমাজের অমঙ্গল”। কিন্তু দণ্ডের যথার্থতাই যদি প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়ায়? আইএসআইয়ের ফলিত রাশিবিজ্ঞানের দুই অধ্যাপকের গবেষণা প্রশ্ন তুলেছে এক দশকেরও বেশি আগের ধনঞ্জয়ের ‘বিরলতম’ অপরাধের তদন্ত প্রক্রিয়াকে নিয়েই। প্রশ্ন তুলেছে, বহুচর্চিত আরুষি মামলার মতো হেতাল পারেখ হত্যাকাণ্ড ‘অনার কিলিং’ নয় তো? তারাশঙ্করের ভাষায় –“কলঙ্কিনী রাধার দণ্ড না দিলে মান থাকে কোথা?” গবেষকদের বিলম্বিত গবেষণা ভিত্তিহীন হতেই পারে। কিন্তু সর্বনাশা সংশয়টা অন্যত্র। যে তদন্তের শাস্তি হিসাবে রাষ্ট্র কেড়ে নিয়েছে জলজ্যান্ত একটা প্রাণ, সে তদন্ত ঘিরে আদৌ কোনো প্রশ্নের অবকাশ থাকবে কেন? কেন থাকবে এক শতাংশ সন্দেহের জায়গাও? “জাজমেন্ট অফ এরর” হলে আর ফেরানো যাবে না মৃত্যুদণ্ডে ঝোলানো দণ্ডিতকে! সে কারণেই অপরাধ করলে কী কারণে অপরাধ করেছে, কোথায় ভুল ছিল এসব না ভেবে, ভুলগুলি শোধরানোর চেষ্টা না-করে অপরাধীকে জেলে ভরা হয়, অথবা হত্যা বা খুন করা হয়। আসলে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে অনেক সমস্যার চটজলদি সমাধান করতে চায় রাষ্ট্রগুলি। কিন্তু একে সমস্যার সত্যিকারের সমাধান হয় না। অপরাধ বন্ধ হওয়া তো দূরের কথা, এক চিলতেও কমে না। মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকলে সেই ভয়ে অপরাধ প্রবণতা কমে যাবে বলে যাঁরা এরকম ধারণার পক্ষপাতী, তাঁদের মৃত্যুদণ্ডবিরোধীরা বলেন– যেহেতু অনেক খুনের ঘটনায় অপরাধী ধরা পড়ে না, দীর্ঘসূত্রী বিচারপদ্ধতি, জুরিদের মতপার্থক্য এবং মৃত্যুদণ্ড প্রদান বিরলতম (rarest of the rare) হওয়ার ফলে নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না যে অপরাধ কমবে। যদি কমত তাহলে মৃত্যুদণ্ড চলছে হাজার হাজার বছর ধরে, এতদিনে অপরাধমুক্ত একটা পৃথিবীতে বাস করতাম আমরা। এখন বসে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে আর্টিকেল লিখতে হত না। তা ছাড়া এমন কোনো পরিসংখ্যান আমাদের জানা নেই, যার দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, মৃত্যুদণ্ড বহাল থাকায় অপরাধ কমেছে বা বন্ধ হয়ে গেছে। এমন কোনো প্রমাণ নেই যে, যে দেশগুলি থেকে মৃত্যুদণ্ড বিলুপ্ত হয়ে গেছে চিরতরে, সে দেশে বিশৃঙ্খলা আর অরাজকতায় ভরে গেছে। বাংলাদেশের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন এক স্ত্রী হত্যার অভিযোগে স্বামীর মৃত্যুদণ্ড দিতে গিয়ে বলেছেন –“এত কঠোর সাজার পরেও কি স্ত্রী হত্যাকাণ্ড বন্ধ হয়েছে? হয়নি। সুতরাং সাজা দিলেই যে দুধের মধ্যে ভালতে থাকবে এমন ধারণা ভুল। আর ফাঁসির দণ্ডও সমাজকে রক্ষা করে না।”
সারা পৃথিবীতে ঈশ্বর বিশ্বাসীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাঁদের বলি আস্থা রাখুন ঈশ্বরের প্রতি। মৃত্যুদণ্ড দিলে তিনিই দেবেন, আপনি নন। আর যাই করুন, কারোকে হত্যা করবেন না। ঈশ্বর কারোকে হত্যা করার অধিকার দেননি, এমন কোনো দলিলও নেই মানুষের হাতে। সুস্থ সমাজের জন্য আপনি বড়োজোর সেই সংশ্লিষ্ট মানুষটিকে সংশোধনের সবরকমের ব্যবস্থা করতে পারেন। আপনার উপযুক্ত করে পুনর্বাসনও দিতে পারেন। যেদিন মানুষ একটা জীবন ফিরিয়ে দিতে পারবে সেদিন মানুষ অবশ্যই জীবন নেবে। একজন অসুস্থ মানুষ হঠকারিতা করে ফেলেছে বলে অন্য একজন সুস্থ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সেই একই হঠকারিতা করবে?
মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে John Bright বলেছেন– “Capital punishment, while pretending to support reverence for human life, does in fact, tend to destroy.” Samuel Romilly বলেছেন “Capital punishments have an inevitable tendency to produce cruelty in people.” Shakespeare বলেছেন –“When punishment exceeds its bounds, the offender’s Scourage is weighed, but never the offence.” ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতের সুপ্রিমকোর্ট বলেছেন– “Deaths caused by an accused should not necessarily end in the end of the accused. Destruction of an individual by the king is not his virtuous act.”
পরিশেষে ইতালির ২৬ বর্ষীয় আইনজীবী মাকুইস সিজার বেক্যেরিয়ার লেখা ‘of Crime and Punishment’ গ্রন্থ থেকে তাঁর বক্তব্য দিয়ে শেষ করি– যেহেতু মানুষ নিজেকে সৃষ্টি করে না, সেহেতু মানুষের কোনো অধিকার নেই কোনো মানুষের জীবন ধ্বংস করার। উপরন্তু কোনো ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তি (রাষ্ট্র) কোনো ক্ষমতা/অধিকার দেয়নি দোষীকে হত্যা করার। তাঁর মতে সাধারণ সময়ে শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ডের প্রয়োজনীয়তা নেই। কারণ এই শাস্তির কোনো প্রতিরোধক প্রভাব নেই সমাজে। প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড দর্শকদের মনে শুধুমাত্র ক্ষণিকের ছাপ ফেলে, তা স্থায়ী ছাপ ফেলতে পারে না। তাঁর ভাষায় –“The death penalty becomes a spectacle and for some of these object of compassion mixed with abhorrence both of these sentiments dominate the minds of the spectators more than the salutory terror which the law wants to inspire.”
———–
সাহায্যকারী তথ্যসূত্র :
(১) রাজা এবং রাষ্ট্রের ধর্ম: দণ্ডনীতির উৎপত্তির গল্প— অধ্যাপক সেলিম রেজা নিউটন, (
২) প্রাণদণ্ড— ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেশ
(৩) মনুসংহিতা (সপ্তম অধ্যায়),
(৪) সেতু– ১৫ জুলাই, ১৯৯৯,
(৫) মানবাধিকার ও সিক্রেট পুলিশ –প্রদীপচন্দ্র বসু,
(৬) লাঞ্ছিত মানবাত্মা– সৌমেন নাগ,
(৭) মাসিক বাঙলাদেশ– মে ২০০৩,
(৮) Wikipedia,
(৯) WikiLeaks,
(১০) অর্থশাস্ত্রম্ –কৌটিল্য,
(১১) দেশ –চিঠিপত্র –৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৩,
(১২) এবেলা –৮ আগস্ট, ২০১৫।
(১৩) of Crime and Punishment– Marquis Cesare Beccaria
(১৪) মৃত্যুদণ্ড ইতিহাস নৈতিকতা বিতর্ক
(সমাপ্ত)