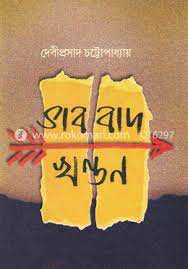- বইয়ের নামঃ ভাববাদ খণ্ডন – মার্কসীয় দর্শনের পটভূমি
- লেখকের নামঃদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
- প্রকাশনাঃ অনুষ্টুপ (ভারত)
- বিভাগসমূহঃ গল্পের বই
০১. ভাববাদ অনুসারে মানুষের মাথা নেই
ভাববাদ অনুসারে মানুষের মাথা নেই
ভাববাদ অনুসারে মানুষের মাথা নেই, তবু বুদ্ধি আছে । কথাটা লেনিনের । আজগুবি শোনালেও উপায় নেই, কেননা সহজ কর্মজীবনের কাছে যা আজগুবি ভাববাদ তাকে ভয় করে না । এই মতবাদ অনুসারে বুদ্ধির অতিরিক্ত বাস্তব বস্তু কোথাও কিছু থাকতে পারে না, তাই মানুষের মাথাও নয়। শুধু বুদ্ধি বা অভিজ্ঞতা বা চিন্তা–যে নাম দিয়েই তার বর্ণনা করা যাক না কেন–সবচেয়ে চরম সত্য। ফলে মাথা নেই, তবু বুদ্ধি আছে। লেনিন বলছেন, এ-যেন এক মাথাহীন দর্শন ।
অথচ, দর্শনের ইতিহাসে এমনই রহস্য যে, মাথা বলে কোনো পদাৰ্থ এই মতবাদ অনুসারে বাস্তব না হলেও একে দেখতে লাগে শুম্ভ-নিশুম্ভের সেই পৌরাণিক সেনাপতির মতো-যার মাথা কেটে ফেললেই মরণ হয় না, কাটা মাথা থেকে ছিটকে-পড়া প্ৰত্যেক রক্তবিন্দু জন্ম দেয় এক একটি সমতুল্য দৈত্যের ।
ভাববাদের এই অদ্ভূত লীলাখেলাকে বর্ণনা করতে বসলে দেশ-বিদেশের নানান পৌরাণিক উপাখ্যান মনে ভিড় করতে চায় ; মনে হয় ভাববাদ বুঝি মিশরের সেই পাখি, যুগে যুগে নিজের ভস্মাবশেষ থেকে যে লাভ করে নবজন্ম ; মনে হয় মৃত দেবতার পুনরুজ্জীবন-কাহিনীতেও অবাক হবার কিছু নেই, কেননা দর্শনের পূত মন্দিরে আপাত তেত্ৰিশ কোটি দেবদেবীর মধ্যে যার উপাসনা প্ৰায় তৈলধারার মতো অবিচ্ছিন্ন, তারও মৃত্যুতে জীবনের পরিসমাপ্তি নয়, নবজীবনের সংকেত ।
কেননা, ভাববাদকে বহুবার বহুভাবে খণ্ডন করা হয়েছে। তবুও মরণ হয়নি তার। বরং যাঁরা চণ্ডবিক্রমে একে খণ্ডন করতে এগিয়েছিলেন, তাঁরাই শেষ পর্যন্ত এর মহিমায় পঞ্চমুখ। শুনতে অবাক লাগে, কিন্তু আগেই বলেছি, আজগুবিকে ভিন্ন করলে, আর যাই হোক, ভাববাদকে বোঝবার জো থাকবে না ।
ভাববাদের যেটা মোদ্দা কথা, সহজ বুদ্ধির সঙ্গে সত্যি যে তার মুখ-দেখাদেখি নেই, আর নেই বলে বর্কালির মতো ভাববাদীকে মাথা খুঁড়ে মরতে হয় ভাববাদের সঙ্গে সহজবুদ্ধির সংগতি প্ৰাণপণে প্রমাণ করতে। সহজবুদ্ধির সাধারণ মানুষ মনে করে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে তার সংসার। কিন্তু ভাববাদী বলবেন, সংসার কোথায় ? আছে তো শুধু সংসারের ধারণা। এদিকে, ধারণার দৌলতে সত্যিই সংসার চলে না : পকেট-বোঝাই ধারণাকে উজাড় করে দিলেও মেছুনী এক টিকলি মাছ দেবে না, কিংবা ফাকা দু’নম্বর বাসের ধারণায় চেপে সাড়ে পাঁচটার সময় অফিস-ভাঙা ভিড় এড়িয়ে আরামে বাড়ি ফেরা, হায়, অসম্ভব । উত্তরে ভাববাদী বিরক্ত হয়ে বলবেন, আসলে মাছটাও যে মাছ নয়, বাড়িটাও বাড়ি নয়, মাছের আর বাড়ির ধারণামাত্র । কিন্তু সহজ মানুষ একেবারো যেন নাচারী-মাছের ধারণা খেয়ে পেট নাকি কিছুতেই ভরে না ! ভাববাদী মাথা না মানলেও এমনতর বেয়াদপির কথা শুনে নিশ্চয়ই মাথা গরম করে বলবেন-আসলে পেট বলে জিনিসটেও যে সত্যি নয়, আর পেট ভরানো বলে ব্যাপারটাও যে নেহাত স্থূল কথা, যাকে ধ্রুব সত্য বলা যায়, তা শুধু পেটের ধারণা আর পেট ভরানোর ধারণা ! এহেন চরম জ্ঞানের কথা শুনেও মানুষের মাথা যদি শ্ৰদ্ধায় নুয়ে না পড়ে, তাহলে সন্দেহ করতে হবে যে, ভাববাদীর রকম-সকম দেখে মাথা বলে জিনিসটা সম্বন্ধেই সে শ্ৰদ্ধা হারিয়েছে ।
তাই বলে সমস্ত যুগের সমস্ত দার্শনিকই যে ভাববাদীর এ-সব কথা মাথা পেতে মেনে নিয়েছেন, তাও মোটেই সত্যি কথা নয়। দর্শনের ইতিহাসে ভাববাদ সম্বন্ধে উৎসাহ যতখানি, ভাববাদকে খণ্ডন করবার উৎসাহ বুঝি তার চেয়ে কম নয়। অনেকবার অনেক দার্শনিক ভাববাদকে খণ্ডন করতে চেয়েছেন । কিন্তু, যেটা সবচেয়ে আশ্চৰ্য কথা, শেষ পৰ্যন্ত তাঁরা নিজেরাই ভাববাদের দীক্ষা নিলেন এবং বিধর্মে দীক্ষিত হবার পর যেন হয়ে দাড়ালেন এক একটি মূর্তিমান কালাপাহাড়,–ভাববাদেরই চরম নৃশংস প্রচারক। ভাববাদ তাই মরেও মরে না, যমালয় থেকে ফিরে আসে নতুন বর নিয়ে, নচিকেতার মতো । একদিকে ভাববাদকে তীব্র, তীক্ষ্ণ আক্রমণ, অপরদিকে সেই ভাববাদের কাছেই করুণ আত্মসমৰ্পণ । এ-কথা যে-সব দার্শনিকের সম্বন্ধে সত্য, তাদের “দুর্বলচেতা” বলে উড়িয়ে দিতে যাওয়া নেহাত আত্মপ্ৰবঞ্চনা হবে । কেননা, দর্শনের ইতিহাসে তাঁরাই হলেন দিকপাল-বিশেষ। স্বদেশে শঙ্কর, প্ৰাচীন গ্রীসে সক্রেটিস, আধুনিক যুরোপে কাণ্ট এবং সাম্প্রতিক যুগে অভিজ্ঞতাবিচারবাদীদের (Empirio-Critics) থেকে শুরু করে প্রয়োগবাদী (Pragmatists), বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী (Realist) ) পৰ্যন্ত-যুগে যুগে এঁরাই তো যুগান্তকারী দার্শনিক বলে স্বীকৃত । অথচ এঁরা সকলেই প্ৰবল উৎসাহে ভাববাদকে খণ্ডন করার পর প্রবলতর উৎসাহেই ভাববাদের মাহাত্ম্যে মেতে উঠেছেন ।
আচাৰ্য শঙ্করের “বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন” ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে সুপ্ৰসিদ্ধ ! ( প্ৰাচীন ভারতীয় দর্শনের পরিভাষায় “বিজ্ঞান’ শব্দটার অর্থ হলো মনের ধারণা, Science নয় ; তাই বিজ্ঞানবাদ আসলে আমরা যাকে ভাববাদ বা Idealism বলে উল্লেখ করছি তাইই। বৌদ্ধ দার্শনিকদের মধ্যে একটি সম্প্রদায় ছিল, যার নাম বিজ্ঞানবাদী এবং যার মতবাদ-ও এমন-কী যুক্তি-প্ৰায় হুবহু য়ুরোপীয় দার্শনিক বার্কলির মতোই ) । এই বিজ্ঞানবাদকে খণ্ডন করতে বসে শঙ্কর, আর যাই হোক, তথাকথিত বৈদান্তিকসুলভ নিম্পূহ সংযমের পরিচয় দেননি, এমন-কী তাঁর ভাষার সহজ প্ৰসাদগুণকে ছাপিয়ে উঠেছে প্ৰত্যক্ষ বিতৃষ্ণ । শঙ্কর বলেন, বিজ্ঞানবাদীর দল যে এমনতর আজগুবি কথা বলতে সাহস পায়, তার আসল কারণ তাদের মুখের মতো অঙ্কুশ নেই ! অর্থাৎ অঙ্কুশের ভয় থাকলে অমন নির্লজ্জ মিথ্যে বলতে তারা সাহস পেত না । শঙ্কর বলছেন, বহির্জগৎকে উড়িয়ে দেবে কেমন করে ? তার অনুভূতি যে অবিসংবাদিত ! দিব্বি এক পেট খেয়ে এবং রীতিমতো পরিতৃপ্ত হয়ে যদি কেউ বলে “কিছুই তো খাইনি, কই পরিতৃপ্তও তো হইনি,”–তাহলে তার কথা যে-রকম মিথ্যে হবে, সেইরকমই মিথ্যে বিজ্ঞানবাদীর কথা । ইন্দ্ৰিয়ের সঙ্গে বহির্বস্তুর সন্নিকর্ষ হবার পর, এবং স্বয়ং অব্যবধানে বহির্বস্তুকে অনুভব করার পর, বিজ্ঞানবাদীও বলে “বহির্বস্তু যে কী, কই তা তো জানি নে, কখনো তা দেখিনি–মনের বাইরে সত্যি কিছু নেই।” বিজ্ঞানবাদীর দল নিজেদের কথাটা হয়তো আর একটু শুধরে নিয়ে বলবে, বিষয়ের অনুভূতিকে আমরা অস্বীকার করতে যাব কেন, আমরা শুধু অস্বীকার করি তার বাহ্যত্বরূপ-বিজ্ঞেয় পদার্থরাশি অন্তর্বর্তী ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। উত্তরে শঙ্কর বলছেন, এ হলো গায়ের জোরের কথা । অনুভূতির সময় আমরা তো এই বলেই অনুভব করি।– এটা হলো স্তম্ভ, ওটা হলো কুড্য । কই এমন তো কখনো অনুভব করিনে যে, এটা হলো স্তম্ভের মানস রূপ, ওটা হলো কুড্যর মানস-রূপ ! তাছাড়া, বহির্বস্তু বলে কোনো জিনিস। যদি কোথাও কোনোকালে না থাকে, তাহলে অন্তর্বর্তী ধারণাকেই বা কেমন করে “বহির্বৎ” হিসাবে অনুভব করা সম্ভব ? আসলে, “বহির্বৎ” বলে ধারণাটা এল কোথা থেকে ? এমন কথা তো মুখ-ফুটে কেউ বলতে পারে না যে, বিষ্ণুমিত্রের চেহারাটা ঠিক বন্ধ্যাপুত্রের মতো !
এই তো শঙ্করের ভাববাদ খণ্ডন। কিন্তু তারপর ? তাঁর নিজের মতবাদ ? ব্ৰহ্ম সত্য, এবং ব্ৰহ্ম মানে বিশুদ্ধ চৈতন্য । এর চেয়ে চরম ভাববাদ-চেতনকারণবাদ-পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনো দেখা দেয়নি । যে বহির্বস্তুর অবিসংবাদিত সত্তা নিয়ে এত তর্ক, তার হলো কী ? সমগ্র জগৎ–যে জগতে ভাববাদীর মুখের মতো চাবুক নেই বলে শঙ্করের এত অনুশোচনা–রজ্জুতে সৰ্প-প্ৰতিভাসের মতো মিথ্যে হয়ে গেল। ( মিথ্যা হিসাবে রজ্জু-সৰ্প আরও এক কাঠি সরেস, কিন্তু তাই বলে ব্যবহারিক পৃথিবী তার চেয়ে এক চুলও বেশি নয়। অদ্বৈত মতে মিথ্যার তারতম্যকে সত্যের তারতম্য বলে ভুল করলে চলবে না ) । সহজবুদ্ধির সঙ্গে সামান্যতম। আপসটুকুও নেই : ভাববাদ-খণ্ডন পরিণতি পেল চুড়ান্ত ভাববাদে।
দর্শনের এই আজব গোলক-ধাঁধায় ঘোরা–ভাববাদের হাত থেকে মুক্তি, পেতে গিয়ে ভাববাদের জালেই জড়িয়ে পড়া–একে শুধু দিশি দার্শনিকের খামখেয়াল বলে উড়িয়ে দেওয়াও চলে না । প্ৰাচীন গ্রীসে মহৎ দার্শনিকের মধ্যেও একই ঘটনার পুনরুক্তি। সক্রেটিসের কথা ধরা যাক। তাঁর দর্শন, এমন-কী তাঁর জীবনকেও বোঝবার একমাত্র সূত্র হলো সফিস্টদের ভাববাদকে খণ্ডন করবার উৎসাহ । সফিস্টরা তর্কে ধুরন্ধর ; তারা প্ৰমাণ করতে চায় যে, ব্যক্তিগত মানুষের মনের ওপরেই পরমসত্তার একান্ত নির্ভর । মানুষের ভালোলাগা-না-লাগাই সত্যবিচারের অভ্রান্ত কষ্টিপাথর। ভাববাদের এই মূল দাবিকে নিছক জ্ঞানের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রেখে সফিস্টদের সন্তোষ নেই, নৈতিক এবং রাজনৈতিক জীবনেও তারা এর জের টানতে চায়–সুনীতি আর দুর্নীতির মধ্যে আসলে কোনো তফাত নেই, আপনার যা রোচে, সেটাই আপনার কাছে সুনীতি ; প্ৰেয় আর শ্ৰেয়, একেবারে নিছক এক । রাষ্ট্ৰীয় আইন-কানুনের বেলাতেও ওই এক কথা-এ-সব আইন-কানুন মানতে যদি মন্দ না লাগে, তাহলে মন্দ কী ? কিন্তু মানতে যে হবেই, এমন কোনো কথা নেই।
সক্রেটিস দেখলেন, ভাববাদের এই দাবি সমাজজীবনের পক্ষে একেবারে দুর্বিষহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ভাববাদকে খণ্ডন করবার জন্যে তিনি প্ৰায় মরিয়া হয়ে উঠলেন । তার খণ্ডন-পদ্ধতি আপাত বিনয়ের পরাকাষ্ঠা, কিন্তু তার পেছনে যে তীব্র বিদ্রুপ আর তীক্ষ্ণ বিদ্বেষ লুকানো, সে-কথা তার ভক্তদের লেখা ভালো করে পড়ে দেখলেই বুঝতে পারা যায়। হাটবাজার থেকে শুরু করে বড়লোকের খানাপিনার আসর পর্যন্ত সর্বত্রই তার দুর্ধর্ষ দ্বন্দ্ব-আহবান,–অমনটাই ছিল তখনকার দিনের ব্যাপার ।
কিন্তু তারপর ? তাঁর নিজের মতবাদ ? তিনি নিজে অবশ্য কোনো দার্শনিক গ্ৰন্থ রচনা করেননি । তাঁর দর্শনের যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায়, তা শুধু তার ভক্তবৃন্দের–প্রধানত প্লেটাে ও জেনোফেন-এর–গ্ৰন্থাবলী থেকে। এবং টীকাকারদের মধ্যে এ নিয়ে অনেক তর্ক আছে যে, প্লেটো নিজের গ্রন্থে সক্রেটিসের মুখে যে দার্শনিক মতবাদ বসিয়েছেন, তা তাঁর গুরুদেবেরই মতবাদ, না নিজের মতবাদ ভক্তিভরে গুরুদেবের নামে প্ৰচারিত মাত্ৰ ! কিন্তু এ-কথা নিয়ে তর্ক যতই থাকুক না কেন, এবং গুরুশিষ্যের মধ্যে মতের প্রভেদ ঠিক কী এবং কতটুকু, এ-বিষয়ে টীকাকাররা নিঃসন্দেহ হতে পারুন আর নাই পারুন,- অন্তত এক বিষয়ে মতভেদের কোনো প্ৰশ্নই ওঠে না ! প্লেটোর দর্শনে সক্রেটিক বিশ্বালোচনের পূর্ণ বিকাশ। এবং গ্ৰীক যুগে প্লেটোর পৌরোহিত্যেই এই ভাববাদের সবচেয়ে জমকালো অভিষেক । ভাববাদ-খণ্ডন এইভাবে ভাববাদেই পরিণতি পেল ।
দর্শনের সেই পুরোনো গোলক-ধাঁধাই ! তবু নেহাত একে প্রাচীনদের সেকেলে ভ্ৰান্তিবিলাস ভেবে নিজেদের সান্ত্বনা দেওয়াও সম্ভব নয়। য়ুরোপের ইতিহাসে বিজ্ঞানের দিগ্বিজয় শুরু হবার পরও যে দিগ্বিজয়ী দার্শনিকের জন্ম হলো, এবং যার বৈজ্ঞানিক বুৎপত্তি অতি-বড় বিপক্ষও অস্বীকার করতে পারেন না, তিনিই বা এই অদ্ভুত আবর্তকে এড়াতে পারলে কই ? ইম্যানুয়েল কাণ্ট–কোএন্স্বের্গের সেই ঋষি ইম্যানুয়েল কাণ্ট,-যাঁর কথা বলতে গিয়ে কোলরিজের কবিকণ্ঠও আবেগে গদগদ হয়ে পড়ে। পাছে তাঁর দার্শনিক মতবাদকে টীকাকারেরা ভুল করে ভাববাদ বলেই চালিয়ে দেন, এই ভয়ে কান্ট তাঁর প্রধান গ্ৰন্থ “শুদ্ধবুদ্ধির বিচার”-এর দ্বিতীয় সংস্করণে একটি নূতন অংশ জুড়ে দিলেন, আর সেই অংশের নাম দিলেন “ভাববাদ-খণ্ডন” । তাঁর মতো পারিপাট্য-প্রিয় দার্শনিক ভাববাদকে খণ্ডন করার সময় এলোমেলোভাবে অগ্রসর হবেন, এমন কথা নিশ্চয়ই ভাবা যায় না ; কাণ্ট এলোমেলোভাবে এগোননি । প্ৰথমে তিনি প্ৰচলিত ভাববাদের শ্রেণীবিভাগ করে নিয়েছেন : একদিকে বার্কলির গোড়া ভাববাদ এবং অপরদিকে দেকার্ত-এর সংশয়াত্মক ভাববাদ । বার্কলি সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য সামান্যই-দেশ এবং কালের বাহ্যসত্তা অপ্ৰমাণ করে, এ দুটিকে মানব অনুভূতির মূল কাঠামো বলে প্ৰমাণ করে, কাণ্ট নাকি আগেই এই গোড়া ভাববাদের মূল উচ্ছেদ করেছেন ( কীভাবে যে তা সম্ভব হয়, তাই নিয়ে অবশ্য টীকাকারদের মধ্যে অনেক বিতর্ক আছে) । আপাতত কাণ্টের প্রধান উদ্দেশ্য হলো দেকার্ত-এর সংশয়াত্মক ভাববাদ খণ্ডন করা । দেকার্ত-মতে একমাত্র আত্মার সত্তাই অবিসংবাদিত সত্য, তাকে সংশয় করতে গেলেও স্বীকার করতে হয়। অপরপক্ষে, বহির্বস্তুর সত্তা ভগবানের দোহাই না দিয়ে মানবার জো নেই। এ কথা খণ্ডন করতে গিয়ে কাণ্ট দেখালেন যে, তথাকথিত অবিসংবাদিত আত্মাকে মানতে গেলে বহির্বস্তুর সন্তা না মেনে উপায় নেই। কেননা, আত্মা সম্বন্ধে আমাদের যেটুকু উপলব্ধি, তা নিছক চেতনা-প্রবাহের উপলব্ধি, এবং প্রবাহকে প্ৰবাহ হিসেবে বুঝতে গেলে স্থির ও নিত্যর সাহায্য নিতেই হবে । কিন্তু স্থির ও নিত্যর কোন হদিশ মানস-জগতে মেলে না । তাই বহির্জগতে তার সত্তা না মেনে উপায়ই নেই । আর এই কথা প্ৰমাণ করার পর কাণ্টে প্ৰায় উল্লাস করে বললেন : ভাববাদীর মরণ-মন্ত্র ভাববাদের বিরুদ্ধেই চেলে দেওয়া গেল, কেননা ভাববাদ অনুসারে একমাত্র অন্তর্বস্তুর যাথার্থই অধিসাংবাদিত, অথচ প্ৰমাণ করে দেওয়া গেল যে, অন্তর্বস্তুর অনুভূতি একান্তভাবে বহির্বস্তুর মুখাপেক্ষী!
ভাববাদ খণ্ডন করলেন কাণ্ট । কিন্তু তারপর ? তাঁর নিজের মতবাদ ? তা নিয়ে অবশ্য টীকাকারদের মধ্যে অজস্ৰ মতভেদ আছে ; এবং মতভেদ এতই বেশি যে, তাঁদের মধ্যেই একজন, একজন শ্ৰদ্ধেয় টীকাকার, শেষ পৰ্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেন যে, কাণ্ট তাঁর সমসাময়িক দর্শনের যে দুৰ্গতির বর্ণনা দিয়েছেন, কাণ্ট-দর্শনের উপর টীকার দুৰ্গতি তার চেয়ে কম নয় । সমসাময়িক দর্শনের দুৰ্গতি বর্ণনা করতে গিয়ে কাণ্ট বলেছিলেন-এ যেন এমন এক মল্লক্ষেত্র, যেখানে কিনা ভুয়ো মারপিটে হাত পাকাবার দেদার সুযোগ ।
কাণ্ট-এর টীকা নিয়ে যে এত শোরগোল, তার আসল কারণ অবশ্য কাণ্ট নিজেই এক অদ্ভুত দোটানায় পড়েছিলেন। একদিকে ভাববাদ খণ্ডন করা সত্ত্বেও ভাববাদের কাছেই করুণ আত্মনিবেদন, অপরদিকে বৈজ্ঞানিক বিবেকের দংশনে অন্তত খিড়কি দোর দিয়ে বস্তুবাদের মূল কথাকে সসংকোচে আমন্ত্রণ। এক বিশেষ যুগের, এক বিশেষ সমাজের জীব হিসাবে কাণ্ট যে কেন এমন দোটানায় পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন, সে প্রশ্নের জবাব মার্কসীয় আলোচনায় পাওয়া যায় ; কিন্তু এ-কথায় কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না যে, তার দর্শনের সচেতন দিকটুকু স্পষ্টই ভাববাদী : তার মতে এই মূর্ত ও দৃশ্য জগৎ বুদ্ধি-নির্মাণ ।
কাণ্ট-এর দর্শনের ঐতিহাসিক পরিণতির দিকে চেয়ে দেখলেও বোঝা যায়, ভাববাদের প্রতি তার দর্শনের ঝোঁক কী দুর্নিবার, কত নিঃসন্দেহ ! উত্তর কাণ্টীয় দার্শনিকেরা কাণ্ট-এর দর্শনকে প্ৰতিজ্ঞ হিসেবে ব্যবহার করে একটানা এগিয়ে চললেন সোজা ভাববাদের পথে । জ্যাকবি, ফিক্টে, হাৰ্বার্ট, সেলিঙ এবং শেষ পর্যন্ত হেগেল। হেগেলের সর্বগ্রাসী পরব্রহ্ম–সে যেন এক চিন্ময়, ভয়ঙ্কর আদিম দেবতা, তার ক্ষুধা কিছুতে মিটতে চায় না, সমগ্ৰ মানব-ইতিহাসকে গ্ৰাস করবার পরও না ।
শুধু ঐতিহাসিক পরিণতির কথাই বা কেন, কাণ্ট থেকে হেগেলীয় ভাববাদে পৌঁছবার পথ যে সোজা, তার নৈয়ায়িক তাৎপৰ্যটুকুও স্পষ্ট ও প্ৰত্যক্ষ । সাম্প্রতিক পরব্রহ্মবাদীরা তাই কাণ্ট থেকেই শুরু করেন এবং শেষ করেন হেগেলে । গ্রীন, কেয়ার্ড, এমন-কী এ যুগের অতবড় ভাববাদী ব্রাডলি পৰ্যন্ত এ কথার ব্যতিক্ৰম নন।
শেষ পর্যন্ত য়ুরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে যেন এক অসম্ভব অবস্থার সৃষ্টি হলো । হেগেলের সর্বগ্রাসী ভাববাদ দার্শনিক মহলে যেন সহজবুদ্ধি হয়ে দাঁড়াল। তাকে প্রমাণ করবার দরকার বুঝি নেই, তাকে খণ্ডন করবার অস্ত্ৰ বুঝি পাওয়া অসম্ভব। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে শুরু করে দার্শনিকেরা অনুভব করতে লাগলেন যে, ভাববাদের আবহাওয়ায় আধুনিক বৈজ্ঞানিক চেতনার শ্বাসরোধ হবার উপক্রম হয়েছে। তাই আবার শোরগোল পড়ে গেলা-ভাববাদকে খণ্ডন করতে হবে, যেমন করেই হোক। দেখা গেল, একের পর এক দার্শনিকের দল মেতে উঠছে ভাববাদকে খণ্ডন করবার উৎসাহে, খোলা হচ্ছে একের পর এক আক্রমণকেন্দ্ৰ । অভিজ্ঞতা-বিচারবাদ ( Empirio Criticism), প্রয়োগবাদ ( Pragmatism ), নব্য-বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ ( Neo-Realism )–এইসব খাঁটি আধুনিক মতবাদ। প্ৰত্যেকটিরই একান্ত উৎসাহ ভাববাদ খণ্ডন। অথচ তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, এইসব অতি-আধুনিক দার্শনিকেরা ভাববাদের বিরুদ্ধে নানা রকম কটূক্তি করবার পরও শেষ পর্যন্ত যেন গোপনভাবে ভাববাদের কথাই আত্মসাৎ করতে চাইছেন ।
অভিজ্ঞতা-বিচারবাদের প্রধান নায়ক হলেন ম্যাক । বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে, নানান রকম দুরূহ পরিভাষার জাদু দেখিয়ে, সাড়ম্বরে তিনি দর্শন শুরু করলেন । এতদিন ধরে চিৎ ও অচিতের মধ্যে যে দুর্লঙ্ঘ্য প্ৰাচীর গড়ে উঠেছে, তাকে ভূমিসাৎ করতে পারলেই নাকি দর্শনের আসল মুক্তি। প্ৰথম কাজ তাই মনোবিজ্ঞান আর পদার্থবিজ্ঞানের মিলন ঘটিয়ে এক বৰ্ণসঙ্করের জন্ম দেওয়া, সেই বৰ্ণসঙ্করেরই নাম হবে দৰ্শন–এবং এই দর্শন অনুসারে জড়পদার্থও পরমসত্তা নয়, মানস-পদার্থও পরমসত্তা নয়, এক তৃতীয় অপক্ষপাতী সত্তা পরমসত্তা। ম্যাক তার নাম দিয়েছেন element, অর্থাৎ মৌলিক সত্তা । অথচ, দর্শনের ক্ষেত্রে এই অভিনব নামধারী আগন্তুকটি, এই তথাকথিত তৃতীয় অপক্ষপাতী সত্তা, আসলে ভাববাদীর পুরাতন মানস-অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়। ম্যাক-প্ৰমুখের এই সাড়ম্বর অতি-আধুনিক দর্শন আসলে বার্কলির মতবাদের ওপর নতুন রঙ চাপিয়ে তাকে অভিনব দর্শন বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টাই। লেনিন তাঁর প্রধান দার্শনিক গ্রন্থে “বস্তুবাদ ও অভিজ্ঞতা-বিচারবাদ”-এ এই বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন । এবং এই সিদ্ধান্ত এমন নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছেন যে, তারপর আর তাই নিয়ে সংশয়ের অবকাশ থাকে না ।
তারপর ধরা যাক প্রয়োগবাদীদের কথা । তাঁদের দর্শনের মূল উৎসাহ যে হেগেলীয় ভাববাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি খোঁজা, এ কথা তাঁরাই জোর গলায় জাহির করছেন। ভাববাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক দর্শন গড়ে তুলতে হলে প্ৰথম দরকার দর্শনের মূল ভিত্তিটারই বদল করা। দর্শনকে আর শুদ্ধবুদ্ধির গজদন্তমিনারে কুমারী ব্ৰতচারিণী করে রাখলে চলবে না, তাকে নামিয়ে আনতে হবে ধুলোর পৃথিবীতে, যেখানে কাজের মানুষের কাঁধ ঘোষাঘোষি, যেখানে প্রয়োগের নগদ মূল্য চুকিয়ে তবেই কিছু কেনা-বেচা । তাই কোন বিশেষ দার্শনিক মতবাদ বা ধারণা, নিছক নিজের জোরে যথার্থও নয়, অযথার্থও নয়,–যাথার্থ্য-দাবির একটি আবেদনমাত্র। ব্যবহারিক জীবনে তার প্রয়োগবৃত্তির ওপর যাথার্থ্য নির্ভর করে ; উক্ত ধারণা বা মতবাদ যদি জীবনে সুখানুভূতির সন্ধান দেয়, তবেই তাকে যথাৰ্থ বলে মানা যাবে, যদি না দেয়, তাহলে বলতে হবে তা ভ্ৰান্ত। হাজার বাকবিতণ্ডায় যে-তর্কের মীমাংসা নেই, প্ৰয়োগের জাদুস্পর্শে নিমেষে তার মীমাংসা হয়ে যায়। এই সহজ কথাটুকু এর আগে দার্শনিকেরা ধরতে পারেননি, তার কারণ এতদিনকার একটানা বুদ্ধিবাদের মোহে তাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন ছিল।
সহজ কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু নতুন কথা কোথায় হলো ? প্রয়োগের প্ৰসঙ্গটা অবশ্যই নতুন, তবু এ তো সুস্থ প্রয়োগের ওপর নির্ভর করা নয়, প্রয়োগের দোহাই-পাড়া মাত্র। কেননা, প্রয়োগবাদীদের মতে এই তথাকথিত প্রয়োগের আসল তাৎপৰ্য শেষ পর্যন্ত ঠিক কী ? সুখানুভূতি-শেষ পর্যন্ত অনুভূতিই, মানস-অভিজ্ঞতাই ! যাথার্থ্য বা সত্যের একান্ত নির্ভর রুচিমাফিক অনুভূতি বা অভিজ্ঞতাই। মানুষের মধ্যে যেটা সবচেয়ে খামখেয়ালী, সবচেয়ে ব্যক্তিগত দিক-তারা ভালো-লাগা-না-লাগা–প্ৰয়োগবাদীর মতে তার উপরই পরমসত্তার চরম নির্ভর । সহজ কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু এমন কিছু নতুন কথা নয়। গ্ৰীক যুগে সফিস্টদের মুখেও এই কথাই শুনতে পাওয়া গিয়েছিল, শোনা গিয়েছিল, সমস্ত সত্যের চরম কষ্টিপাথর হলো ব্যক্তিগত মানুষের ভালো-লাগা-না-লাগা ; কেবল তারা এমন আধুনিক ভাষায় প্রয়োগ শব্দের দোহাই দিতে জানতেন না । ভাববাদের পুরোনো কথাটুকুই, কেবল বাইরের দিকটাই নতুন। শুধু নবকলেবর।
ভাববাদীর ভাষা যেন গঁদের সঙ্গে করাতগুঁড়ো মিশিয়ে একটু ঘন করা হয়েছে, বললেন সাম্প্রতিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী । অন্তত সাত সাতটা সরল অনুপপত্তির ওপর ভাববাদের ভিত, বললেন নব্য-বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীর দল। মনে হয়, মেজাজটা এবার রীতিমতো কড়া, আশা হয় এবার আর কোনো রকম আপসের কথাই উঠবে না। ঠিক হলো, ভাববাদকে খণ্ডন করতে হবে রীতিমতো দল পাকিয়ে, সভা ডেকে । সভা ডাকলেন নব্য বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা ; সভা ডাকলেন বৈচারিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীর দল-বড় বড় নামজাদাদের সভা । ঠিক হলো, এমন-কী ন্যায়শাস্ত্রকেও সমূলে সংস্কার করতে হবে-পুরোনো ন্যায়শাস্ত্রের আবর্জনায় ভাববাদের আগাছা জন্মেছিলো, তাই সংস্কৃত বৈজ্ঞানিক নব্যন্যায় চাই। প্ৰবর্তিত হলো “গাণিতিক” নব্যন্যায় ।
অনুষ্ঠানের এতটুকুও ত্রুটি নেই। আয়োজন দেখে মনে হয়, ভাববাদের পরমায়ু এবার সত্যিই শেষ হবে। ভাববাদ তবুও যেন মিশরের সেই পৌরাণিক পাখিই, নিজের ভস্মাবশেষের মধ্যেই তার নবজন্মের নিঃসন্দেহ সুচনা । সাম্প্রতিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের এত তোড়জোড়, এত শোরগোল, শেষ পৰ্যন্ত তারও পরিসমাপ্তি ভাববাদেই ! জানি, একথা প্ৰমাণ করা পরিসরসাপেক্ষ, বিশেষত এই কারণে যে, সাম্প্রতিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা জানেন, নিজেদেরওই গোপনভাববাদকে ঢাকবার জন্য জটিল তর্ক আর দুরূহ পরিভাষার ঠাসবুনোনি দিয়ে কী অপূর্ব আচ্ছাদন বুনতে হয়। সহজ কথাকে কঠিন করে প্রকাশ করবার দুর্লভ মেধা তাদের। সুখের বিষয়, মরিস কর্নফোর্থ তার গ্ৰন্থ “বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে ভাববাদ”- এ এই আচ্ছাদনকে ছিন্নভিন্ন করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, অত দুরূহ জটিলতার পেছনে মোদ্দা কথাটুকু বার্কলিরই কথা । সাম্প্রতিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের তথাকথিত গাণিতিক নব্যন্যায়ের স্বরূপও তিনি উদঘাটন করেছেন । আসলে সাম্প্রতিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা এই নব্যন্যায়-এর চারপাশে এমন দুৰ্বোধ্যতার আর জটিলতার আবহাওয়া সৃষ্টি করেছেন যে, সাধারণ পাঠক একে দূর থেকে সন্ত্রম করেন, কাছ-ঘোষবার সাহস বড় কারুর হয় না। কর্নফোর্থ এর গ্ৰন্থ পড়ার পর বুঝতে পারা যায়, এ যেন এক অতি আধুনিক দিল্লির লাডু-শুধু যে না-খেলেই পস্তাতে হয় তাই নয়, খেতে গেলেও পস্তাতে হয়, কেননা খেতে গেলে শুধুই দাঁত ভাঙে, কিন্তু ভাববাদের চর্বিতচর্বণ ছাড়া নতুন কোনো আস্বাদ জোটে না।
কর্নফোর্থ এর গ্রন্থ ছাড়াও এখানে শুধু একটা উদাহরণ দেওয়া যাক । সাম্প্রতিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের গুরুদেব হলেন ইংরেজ দার্শনিক মূরি। “ভাববাদ খণ্ডন” নামে তাঁর ছোট প্ৰবন্ধ হালের য়ুরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে নাকি যুগান্তর এনেছে। উত্তর-বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীরা সকলেই তার কাছে প্ৰত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঋণী। ভাববাদের বিরুদ্ধে গালিগালাজ করবার সময় মুর-এর কণ্ঠ সতেজ, যুক্তি যেন দুর্ধর্ষ। জ্ঞানের বিষয় জ্ঞাতার মনের ওপর নির্ভর করে, এ কথা বলা, মূর-এর মতে, নেহাতই নির্বোধের লক্ষণ। কিন্তু এ সমস্তই তো নেতিবাচক কথা। প্রশ্ন ওঠে, জ্ঞানের বিষয় তাহলে ঠিক কী রকম ? উত্তরে মূর ইন্দ্ৰিয়োপাত্ত (Sense-datum) নামের এক জাতীয় সত্তার আমদানি করলেন । এই ইন্দ্ৰিয়োপাত্ত হল দর্শনের জগতে অভিনব-তম আজব-চিড়িয়া, অভিজ্ঞতাবিচারবাদীর element-এর সাক্ষাৎ বংশধর । লেনিন দেখিয়েছিলেন, element জিনিসটা বার্কলির percipii ছাড়া আর কিছুই নয়। মুর-এর ইন্দ্ৰিয়োপাত্তর বেলাতেও হুবহু একই কথা । এই ইন্দ্ৰিয়োপাত্তর স্বরূপ নিৰ্ণয় করা নিয়ে যতই তিনি মাথা ঘামিয়েছেন, ততই তাঁকে বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদ ছেড়ে পেছু হটতে হয়েছে। বার্কলি-হিউমের ভাববাদের দিকে। মুর-এর দর্শনে এই যে বিপৰ্যয়, একে নিছক তাঁর ব্যক্তিগত খেয়ালখুশিও বলা চলে না ; সাম্প্রতিক বস্তুস্বাতন্ত্রাবাদীরা প্ৰায় প্ৰত্যেকেই এই দিক থেকেও গুরুদেব মূর-এর চরণচিহ্ন অনুধাবন করেন। জ্ঞানবিজ্ঞান (Epistemology) নিয়ে তাঁদের অন্য অজস্র বিতর্কের পেছনে তাই ভাববাদেরই বিচ্ছুরিত হাসি ।
প্ৰাচীন মিশরে দেবতা আসিরিসের জীবন-মরণ-কাহিনী নিয়ে প্ৰতিবছর মরমী নাট্যের অভিনয় হতো। দেবতার পীড়ন, দেবতার মৃত্যু, তারপর আবার দেবতার পুনরুজ্জীবনের পর দেবতা দেখা দিতেন হয় তাঁর নিজের মূর্তিতেই, আর না হয় তো পুত্র হোরাস-এর মূর্তিতে। কিন্তু মূর্তি যারই হোক, মূলে সেই দেবতাই, সেই অসিরিস। দর্শনের ইতিহাসেও যেন একই নাটকের অভিনয় । ভাববাদের পুনরুজ্জীবনও চিরকাল একই মূর্তিতে নয়, কিন্তু বিভিন্ন মূর্তির মধ্যে আপাত পার্থক্য যতই হোক না কেন, মূলে সেই পুরাতন ভাববাদই । তাই পূর্বপক্ষ এ কথা বলতে পারবেন না যে, একজাতীয় ভাববাদ খণ্ডন করে শঙ্করপ্রমুখ দার্শনিকেরা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জাতের ভাববাদ প্রবর্তন করেন। আসলে বিভিন্ন ভাববাদের মধ্যে বৰ্ণভেদটুকু আপাতত যতই গুরুত্ব বলে মনে হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত তা নেহাতই অগভীর। একথা মূর এবং পেরীর মতো দার্শনিকদের দৃষ্টিও এড়ায়নি, যদিও তারা যে যুক্তি দিয়ে কথাটা প্ৰমাণ করবার চেষ্টা করেন, সে যুক্তি শেষ পর্যন্ত বিচারসহ নয়। ভাববাদের সামাজিক উৎস নিয়ে আলোচনা করবার সময় এ বিষয়ে দীর্ঘতর মন্তব্যের অবকাশ পাব ।
০২. ভাববাদকে খণ্ডন করা যায়নি
অনেক নামকরা দার্শনিক, অনেক রকম যুক্তি-তর্ক দিয়ে ভাববাদকে অপ্ৰমাণ করতে চেয়েছেন। তবু ভাববাদকে খণ্ডন করা যায়নি। বরং একে খণ্ডন করবার জন্য বুদ্ধির জৌলুশে দীপ্ত যে-সব দার্শনিক প্রায় মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন, শেষপৰ্যন্ত র্তারা ভাববাদের স্নিগ্ধচ্ছায়াতেই ক্লান্ত দার্শনিক চেতনা এলিয়ে দিলেন। যেন ভাববাদই একমাত্র আর অনিবাৰ্য দার্শনিক মতবাদ, যেন মানুষের বুদ্ধি এই চূড়ান্ত অসম্ভবের পায়ে যুগ যুগ ধরে মাথা কুটেছে, তবু মুক্তি পায়নি। তার দাসত্ব থেকে।
আসলে, একদিক থেকে বাস্তবিকই তাই। শুধু বুদ্ধি দিয়ে ভাববাদকে খণ্ডন করা যায় না-যে-দর্শন বুদ্ধির দাবিকে, বিশুদ্ধ চেতনার দাবিকে চরম দাবি বলে দেখতে চায়, সে-দর্শন শেষ-পৰ্যন্ত ভাববাদেই পরিসমাপ্তি পেতে বাধ্য। তাই শুধু তর্ক-বলে ভাববাদকে অস্বীকার করতে গেলে শেষ-পর্যন্ত তর্কের খাতিরেই ভাববাদকে স্বীকার করতে হয়। একথা নৈয়ায়িকভাবে অনিবাৰ্য, এবং এর সামাজিক কারণটুকুও স্পষ্ট।
নৈয়ায়িকভাবে কেন যে অনিবাৰ্য, প্রথমে তা-ই আলোচনা করা যাক। সামাজিক ভিত্তির কথা প্ৰথমেই তোলা উচিত; তবুও পরে তোলাই ভালো। কেননা পণ্ডিতমহলের এতদিনকার একটানা প্রচারের ফলে দর্শনের সাধারণ ছাত্রের পক্ষে দার্শনিক বিচারে নিছক নৈয়ায়িক সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে মেনে নেওয়া আজ প্ৰায় অভ্যাসে পরিণত। তাই শুরুতেই সামাজিক উৎসের কথা প্ৰতিবন্ধ হয়ে দাড়াতে পারে। আমাদের প্রাচীনেরা বলতেন। “শাখা চন্দ্র-স্যায়”-চাদ যদি গাছের আড়ালে থাকে, তাহলে প্ৰথম চেষ্টাতেই সে চাদ কাউকে দেখানো হয়তো কঠিন; তাই গাছের সেই শাখার দিকেই প্ৰথমে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হয়। দার্শনিক আলোচনাতেও তাঁরা এইভাবে অগ্রসর হবার নির্দেশ দিয়েছেন। যে-কথা শুনতে শ্রোতার অভ্যাস আছে, সেই কথাতেই আলোচনার সূত্রপাত হওয়া উচিত, পরে যে-কথায় তিনি অনভ্যস্ত, সেই কথার দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া ভালো। কেবল মনে রাখতে হবে, লোকায়তিক দৃষ্টিতে নিছক নৈয়ায়িক আলোচনা অর্থহীন ও অবাস্তর; মূর্ত সামাজিক পরিপ্রেক্ষা থেকে বিচ্ছিন্ন হলে, লৌকিক জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োগ থেকে বিচুত হলে, দার্শনিক আলোচনা-তা সে যতই যুক্তিকণ্টকিত ও আপাতপাণ্ডিত্যপূর্ণ হোক না কেন-কাকদন্ত পরীক্ষার মতো বৃথা হতে বাধ্য। কেননা দর্শন শুধু শৌখিন মানুষের অবসর বিনোদন নয়, শ্রেণীসংগ্রামের অস্ত্ৰও। এতদিন পর্যন্ত পরোক্ষভাবে তাই হয়ে এসেছে, আজকে প্ৰত্যক্ষভাবে হবার দিন এসেছে। কিন্তু শুরুতেই এসব কথা প্ৰতিবন্ধ সৃষ্টি করবে। আপাতত শাখাকে চন্দ্ৰ মনে করেই অগ্রসর হওয়া যাক, আলোচনা করা যাক, তর্ক-বলে কেন যে ভাববাদকে খণ্ডন করা সম্ভব নয়, তার নৈয়ায়িক অনিবাৰ্যতা নিয়ে।
তর্ক বলে, শুধু বুদ্ধি দিয়ে, ভাববাদকে খণ্ডন করা অসম্ভব; এ প্রচেষ্টা স্ববিরোধী, অতএব আত্মঘাতী। বুদ্ধি দিয়ে খণ্ডন করতে গেলে মেনে নিতে হবে বুদ্ধির দাবি-তর্কের দাবি, চেতনার দাবি-চরম দাবি; মানতে হবে, এ দাবি মেটাতে পারে না বলেই আলোচ্য মতবাদ সমর্থনের অযোগ্য। তর্কমূলক খণ্ডনের আর কী মানে হওয়া সম্ভব? কিন্তু ওটুকুকে স্বীকার করা মানেই ভাববাদকে স্বীকার করা। কেননা, ভাববাদের মূল কথাও ওই একই; চেতনার দাবিই চরম দাবি; চেতনাই প্ৰাথমিক ও পরম সত্য। এ-কথাকে। নানানভাবে প্ৰকাশ করা হয়েছে। অভিজ্ঞতা বা চেতনা বা বুদ্ধি বা মন,- বা অমাজিত মানুষের কাছে খটকা লাগে, এই ভয়ে যার নাম দেওয়া হয়েছে ভগবান-যে-কোন শব্দ দিয়েই একে বর্ণনা করা যাক না কেন, তাকেই পরমসত্তা বলে মানতে হবে, তার দাবিই চরম দাবি, তার উপর নির্ভর করে। বলেই বাস্তব হলো বাস্তব, তার উপর যা নির্ভর করে না তার নাম অলীক। তাই মানা চলবে না চেতনা-নিরপেক্ষ কোনো জড়পদার্থকে, বলতে হবে বস্তুর ধারণা নেহাতই নামমাত্র সত্য (বার্কলির নামমাত্রবাদ)।
দর্শনের মূল প্রশ্ন হলো : বুদ্ধির কাছে যে দাবি প্রাথমিক ও মৌলিক, পরমসত্তা কি সেই দাবি মেটাতে বাধ্য? ভাববাদী বলবেন : নিশ্চয়ই; সেটুকুই তো আমাদের দর্শনের সচেতন ভিত্তি; এবং শুধু আমার দর্শনের কেন, যারা আমার কথা মানেনও না, তারাও এই ভিত্তিটুকুকে অচেতনভাবে স্বীকার করে নেন। তাই ভাববাদকে খণ্ডন করতে গিয়ে যদি কেউ ভাববাদের এই মূল কথাটুকুই মেনে নেন, যদি আশা করেন তর্কবলে ভাববাদকে খণ্ডন করা সম্ভব হবে, — অর্থাৎ, দেখানো যাবে, তর্কের দাধি মেটাতে পারে না বলেই ভাববাদ ভ্ৰান্ত-তাহলে ভাববাদীর পক্ষে এতটুকুও বিচলিত বোধ করবার কারণ নেই। ভাববাদী জানেন, যে-পূর্বপক্ষ বুদ্ধির দাবিকে চরম দাবি বলে মেনে নিয়েছে, সে-পূর্বপক্ষ সাপও নয়, সাপিনীও নয়, শুধু ফোঁস-ফোঁস; নেহাতই পোষা সাপ, যে-সাপ কখনো ছোবল দেবে না।
তর্কের উপর বিরূপ হয়েছেন অনেক দার্শনিক, বুদ্ধি সম্বন্ধে বিতৃষ্ণ হয়েছেন অনেকে। তাঁরা কেউবা ধরেছেন নিবুদ্ধির পথ, কেউবা অতিবুদ্ধির। এঁদের কথা আলোচনা করলে দেখা যাবে, শ্রেণীর দাবি আর যুগের দাবি মেটাতে গিয়ে বুদ্ধির যেটুকু আসল অবদান, সেটুকুকেই এরা কেমনভাবে অস্বীকার করেন, আর কেমনভাবে মেনে নেন, শুদ্ধবুদ্ধির যেটা আসল গ্লানি, তাকেই। আপাতত দেখা, যাক কোনো কোনো দার্শনিক কী রকম স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে অনুভব করেছেন, শুধু তর্কবলে ভাববাদকে খণ্ডন করা যায় না। দৃষ্টান্ত হিসেবে ফরাসী দার্শনিক দিদারো এবং ইংরেজ দার্শনিক রাসেল-এর উল্লেখ করা যায় {
রাসেল বলছেন (মনে রাখতে হবে, রাসেল হলেন সাম্প্রতিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের একজন প্রধান, আধুনিক দর্শনের ইতিহাসে একজন প্ৰধান বর্ণচোরা ভাববাদী) : “একদিক থেকে মানতেই হয় যে, আমরা নিছক নিজেদের সত্তা এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা ছাড়া অন্য কোনো বস্তুর সত্তা প্ৰমাণ করতে পারি না। পৃথিবীতে শুধু আমরা এবং আমাদের চিন্তা, অনুভূতি ও ইন্দ্ৰিয়বেদনা ছাড়া আর যে কিছুই সত্য নয়, বাকি সবই যে আমাদের কল্পনামাত্ৰ, এই অর্থপত্তি থেকে কোনো নৈয়ায়িক অসম্ভাবনা হয়তো ঘনায় না। –সমস্ত জীবনটাই যে একটা স্বপ্ন, সে স্বপ্নে আমাদের সামনে যা কিছু ঘটছে তা আমাদেরই সৃষ্টি, এ কথা ভাবার মধ্যে কোনো নৈয়ায়িক অসম্ভাবনা নেই। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রের দিক থেকে যদিও এ কথা অসম্ভব নয়, তবুও একে সত্যি বলে মানবার কোনো রকম কারণ নেই।”
যদিও নৈয়ায়িকভাবে অসম্ভব নয়, তবুও একে মানবার কোনো তাগিদ। নেই-কথাটা একদিক থেকে ঠিক। অধিবিদ্যার বিশুদ্ধ বুদ্ধি দিয়ে ভাববাদকে খণ্ডন করা না গেলেও ভাববাদকে মানবার কোনো তাগিদ বাস্তবিকই নেই, কেননা প্রয়োগের ক্ষেত্রে ভাববাদের অন্তঃসারশূন্যতা একেবারে প্রকট হয়ে পড়ে। কিন্তু রাসেল তো আর সে-দিকে এগোননি। বরং তিনি আগে থাকতে উলটো সুর গেয়ে উলটোভাবে গোড়া বেঁধে রাখতে চেয়েছেন, আগে থাকতে তিনি বলে রেখেছেন-দার্শনিক হবার বাসনা থাকলে আজগুবিকে ভয় করলে চলবে না (দার্শনিক হবার বাসনা, না ভাববাদী হবার বাসনা?)। তাই আমাদের দেশের ন্যায়-সূত্রকার রাসেল-এর মুখে এমনতর কথা শুনলে নিশ্চয়ই উৎসাহিত হয়ে উঠতেন। কেননা, তিনি যে অনুপপত্তির নাম দিয়েছেন ‘বিরুদ্ধ, তার দৃষ্টান্ত অপেক্ষাকৃত বিরল, এবং রাসেল-এর এই উক্তি সেই অনুপপত্তির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সিদ্ধান্তমত্যুপেত্য তৎবিরোধী বিরুদ্ধ : রাসেল-এর অজস্র অস্থিরমতিত্ব সত্ত্বেও সমস্ত দর্শন ধরে তিনি শুদ্ধ ন্যায়শাস্ত্রের দাবিকে, প্রয়োগ-জীবনের সঙ্গে লেশ সম্পর্কহীন বিশ্লেষণের দাবিকে চরম দাবি বলে ঘোষণা করেছেন; আর তা সত্ত্বেও কিনা হঠাৎ বলে বসেছেন, ভাববাদ খণ্ডন এ দাবিকে মেটাতে না পারলেও অস্বীকাৰ্য নয়!
তর্কবলে ভাববাদকে যে অপ্ৰমাণ করা যায় না, এ কথায় রাসেল-এর অবশ্য তেমন কোনো বিক্ষোভ নেই, হাজার হোক রাসেল হলেন ম্যাক-আভেনেরিয়সের দার্শনিক বংশধর, প্ৰচ্ছন্ন ভাববাদীই। কিন্তু ফরাসী দার্শনিক দিদারো-র পক্ষে অত সহজে এই কথা স্বীকার করা কঠিন। তিনি মনেপ্ৰাণে বস্তুবাদী, ভাববাদের কবল থেকে তাঁর মুক্তি-প্ৰয়াসের মধ্যে ফাকি নেই। তাই, তর্কবলে ভাববাদের অসম্ভাবনাকে অপ্ৰমাণ করা যাচ্ছে না দেখে তার যে আক্ষেপ ও অসহিষ্ণুতা, সেটা লক্ষ করবার মতো :
“যে-সব দার্শনিকেরা শুধু নিজেদের অস্তিত্ব এবং নিজেদের মনের মধ্যে ইন্দ্ৰিয়-পরম্পরার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে বাকি সমস্ত কিছুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করেন, তঁদেরই নাম ভাববাদী! এ হলো এক রকমের দার্শনিক নবাবিয়ানা, আমার তো মনে হয় শুধুমাত্র অন্ধ মানুষ এরকম দর্শনের জন্ম দিতে পারে; তবুও মানুষের বুদ্ধির আর দর্শনের গলায় দড়ি, এ মতবাদ সবচেয়ে আজগুবি হলেও একে খণ্ডন করা সবচেয়ে দুরূহ।”
দিদারো-র এই উক্তি উদ্ধৃত করে লেনিন বলছেন, দিদারোই সাম্প্রতিক বস্তুবাদের খুব বেশি কাছ ঘোষতে পারেন, কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, শুধু তর্ক বা শুধু যুক্তি দিয়ে ভাববাদকে খণ্ডন করা যায় না, কেননা এখানে আসল কথা তর্কাতর্কির কথাই নয়।
নিছক তর্কবলে ভাববাদকে যে খণ্ডন করা যায় না, এ কথা প্ৰমাণ করবার জন্যে শুধু দুচারজন দার্শনিকের স্বীকৃতির উপর নির্ভর করবার দরকার নেই। সাম্প্রতিক দর্শনে বুদ্ধিমূলক ভাববাদ খণ্ডনের চরম দৃষ্টান্তকে বিশ্লেষণ করা যাক; দেখা যাবে, বিপক্ষের অনেক বাকময় শরের শয্যায় শুয়েও ভাববাদ কী-রকম অক্ষত দেহে কী অক্ষুন্ন আয়াস উপভোগ করতে পারে। স্থানাভাবের দরুন এখানে মাত্র একটি দৃষ্টান্ত তুলব।–সাম্প্রতিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের ভাববাদ খণ্ডন। সাম্প্রতিক দর্শনে সেইটিই প্ৰধান দৃষ্টান্ত। মনে রাখতে হবে, আমাদের দেশের প্ৰাচীনেরা বলেছেন, ‘প্রধান-মল্প-নিবৰ্হিণ ন্যায়’। মল্পক্ষেত্রে বিপক্ষ হিসেবে প্ৰধান মল্লকে যদি পরাভূত করা যায়, তাহলে ছোটখাট মল্পের সঙ্গে আর আলাদাভাবে লড়বার দরকার পড়ে না। দার্শনিক দ্বন্দ্বের বেলাতেও সেই রকম।
সাম্প্রতিক দর্শনে বস্তুম্বাতন্ত্র্যবাদীর ভাববাদ খণ্ডন নিয়েই শোরগোল সবচেয়ে বেশি। এবং বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের মধ্যে প্ৰধান হলেন শ্ৰীযুক্ত মূর–ভাববাদের বিরুদ্ধে তিনি যে সুর শুরু করেছেন, বাকি সব বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী মোটামুটি তারই ধুয়ো ধরেন,–যদিও নানান ভাবে, নানান ভঙ্গিমায়। তাই মুর-এর যুক্তিটাই প্ৰথমে ধরা যাক। মূর বলেন, ভাববাদ–তা সে যে-জাতেরই হোক না কেন, –প্রেরণা পেয়েছে বার্কলির সেই সরল উক্তি থেকে–সত্তার সার-পরিচয় তার অভিজ্ঞতায়। কিংবা, যা একই কথা, অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ কোনো বস্তুর সত্তা অভাবনীয়।
মূর বলেন, অতি সরল এক অনুপপত্তির উপর এই মতবাদের প্রতিষ্ঠা। যে-কোনো অভিজ্ঞতাকে বিশ্লেষণ করলে দুটি স্বতন্ত্র উপাদান পাওয়া যাবে। – এক হলো চেতনা, যার সঙ্গে সমস্ত ইন্দ্ৰিয়বেদনার সম্পর্ক; আর এক হলো চেতনার বিষয়, যার দরুন। এক অভিজ্ঞতা অন্য অভিজ্ঞতা থেকে ভিন্ন। ‘লালরঙ” সম্বন্ধে জ্ঞান এবং “নীল-রঙ” সম্বন্ধে জ্ঞান,-এ দুয়ের মধ্যে প্ৰভেদ স্পষ্ট, এবং এ প্ৰভেদের কারণ বিষয়ের বিভিন্নতা ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। আবার জ্ঞান হিসেবে দুটির মধ্যে সাদৃশ্য, সে সাদৃশ্যের কারণ উভয়ের মধ্যে চেতনার বিদ্যমানতা। তাই, চেতনার বিষয় এবং বিষয়ের চেতনা, এ দুয়ের মধ্যে তফাত করতেই হবে; অথচ সেই প্ৰভেদকে অস্বীকার করার উপরই ভাববাদের আসল ভিত্তি। চেতনার বিষয় ও বিষয়ের চেতনা-এ দুয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক, তারই নাম “জ্ঞান” বা “সচেতন হওয়া”। এ সম্পর্ক আদি ও অপূর্ব, এর জুড়ি আর কোথাও মিলবে না। তাই, নীল রঙ সম্বন্ধে যখন জ্ঞান হচ্ছে, তখন এ কথা বলা চলবে না যে, আমাদের চেতনায় নীল-রঙ-এর প্রতিবিম্ব পড়ছে, কেননা এখানে আসলে জ্ঞান হচ্ছে নীল-রঙ-এর জ্ঞান সম্বন্ধেই।
মূর এর ছোট প্ৰবন্ধ “ভাববাদ খণ্ডন”, তাতে যুক্তির জৌলুশকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু কথা হলো, সে-যুক্তির গভীরতা কতটুকু? সে-যুক্তি কি সত্যিই ভাববাদের যুক্তিকে খণ্ডন করতে পারে? ভাববাদীর যুক্তি অত্যন্ত সরল ও অত্যন্ত স্পষ্ট; চেতনার বা জ্ঞানের গণ্ডির মধ্যে পড়ছে না। এমনতর। কোনো বস্তু বা বিষয়কে আমরা কি জেনেছি? এ প্রশ্নের রকম থেকেই উত্তরটুকু সহজ হয়ে পড়ে – জানা মানেই চেতনার বা জ্ঞানের গণ্ডীভূত হওয়া; তাই যা চেতনার গণ্ডীভূত নয়, তাকে জানিবার কথাই ওঠে না। ভাববাদী বলবেন, যা কিছু আমরা জানি, তা সমস্তই চেতনার উপর নির্ভরশীল, কেননা তা অনিবাৰ্যভাবেই চেতনার গণ্ডীভূত, চেতনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য-সম্বন্ধযুক্ত। চেতনার উপর নির্ভরশীল হওয়া মানেই মানসিক”। অর্থাৎ, আমরা যা কিছু জানি, তা সমস্তই মানসিক। এবং দর্শনে এমন কোনো কিছুকে নিশ্চয়ই বাস্তব বলে মানা চলবে না, যার সম্বন্ধে আমাদের কোনো জ্ঞান নেই। এ কথাও তো অত্যন্ত সহজ কথা; যাকে জানা যায়নি, তাকে সত্যি বলে স্বীকার করবার অধিকার দার্শনিকেরও থাকতে পারে না। তাই, দার্শনিক বিচারে শুধু চেতনানির্ভর বস্তুকে, শুধু মানসিক সত্তাকে একমাত্র সত্য বলে মানতে হবে। অর্থাৎ পরমসত্তা মানসিক, অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ নয়।
ভাববাদীর মূল যুক্তিকে উপরোক্তভাবে বর্ণনা করায় হয়তো অতি-সারল্যের অপবাদ জুটবে। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখতে গেলে দেখা যাবে, আসল যুক্তিটা এ ছাড়া কিছুই নয়। উদাহরণ হিসেবে বার্কলি এবং বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধর কথা ধরা যায়; এঁদের যুক্তিই ভাববাদের প্রাঞ্জলতম নিদর্শন।
বার্কলি বলছেন : “মানব-জ্ঞানের বিষয়াবলীকে যিনিই প্ৰেক্ষণ করেছেন, তাঁর কাছেই এ কথা স্পষ্ট যে, সেগুলি হয় ইন্দ্ৰিয়ের উপর বাস্তব ধারণার ছাপ, না-হয় নিজেদের মনের বাসনা ও ক্রিয়া সম্বন্ধে অনুভূতি, আর না-হয় স্মৃতি ও কল্পনাশক্তির দ্বারা গড়া ধারণামাত্র–“সকলেই মানবেন, আমাদের মনের চিন্তা, বাসনা বা কাল্পনিক ধারণার কোনোটাই মানস-নিরপেক্ষ হতে পারে। না। এবং সে-কথার চেয়ে আমার কাছে এ-কথা একটুও অস্পষ্ট নয় যে, আমাদের বিভিন্ন অনুভূতি ও ইন্দ্ৰিয়ের উপর ছাপা ধারণাগুলিকে যেমনভাবেই একসঙ্গে মিশেল করা হোক না কেন (অর্থাৎ, সেগুলি দিয়ে যে-কোন রকম বিষয়ই গড়া যাক না কেন), এগুলি অভিজ্ঞতাকারী-মন-নিরপেক্ষ হতেই পারে না।” বার্কলির যুক্তি আধুনিক পাঠকের কাছে অতি প্ৰসিদ্ধ, তাই এর দীর্ঘতর উদ্ধৃতি অবাস্তর হবে।
বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বলছেন, জ্ঞান ও বিষয়ের মধ্যে সহোপলম্ভ নিয়ম বর্তমান, অর্থাৎ একটিকে ছাড়া অপরটিকে পাবার কোনো উপায় নেই। জ্ঞান ব্যতীত একেবল বিষয়, বা বিষয় ব্যতীত কেবল জ্ঞান কেউ কখনও অনুভব করতে পারে না। এই সহোপলম্ভ নিয়ম থেকেই জ্ঞান ও বিষয়ের মধ্যে অভেদ সিদ্ধ হতে বাধ্য, এবং এই অভেদকে মানা মানেই বাহাবস্তুকে অস্বীকার করা-জান এবং জ্ঞানের বিষয় যদি একই হয়, তাহলে বাহুবিস্তুর স্থান আর কোথায়? এই অভেদভাবের প্রতিবন্ধক বা বিরুদ্ধ প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না, এমন দৃষ্টান্ত অসম্ভব যেখানে জ্ঞানের বিষয় হিসেবে জ্ঞান-নিরপেক্ষ বাহবিস্তু রর্তমান। বরং বাহবিস্তুকে যারা স্বীকার করেন, যারা বলেন বাহবিস্তু না থাকলে জ্ঞানের বিষয়ই থাকে না, অতএব জ্ঞানই সম্ভব হয় না, তাদের কথার বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত মোটেই দুর্লভ নয়। অর্থাৎ, এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যেখানে বাহবিস্তু সত্যিই নেই, অথচ তদাকার জ্ঞান হচ্ছে। যেমন স্বপ্নদর্শন, মায়াদর্শন, মরুমরীচিকায় জলদর্শন, আকাশে গন্ধৰ্বনগর দর্শন, এইরকম কতই তো দৃষ্টান্ত! এখানে জ্ঞানই জ্ঞানের বিষয়, জ্ঞানই পূর্বক্ষণে বাহাবস্তুর আকার ধারণ করে এবং দ্বিতীয়ক্ষণে বিষয়ের গ্রাহকাকার ধারণ করে। অতএব, জ্ঞানের পক্ষে বিষয় ও বিষয়জান উভয়ের আকার ধারণ করা। এমন কিছু অসম্ভব কথা নয়। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বলছেন,-বাহপদার্থকে যদি মানা যায়, তাহলে বিভিন্ন জ্ঞান কেমন করে পরস্পরের থেকে ভিন্ন হতে পাৱে? কিন্তু এই প্রশ্নের জবাব এমন কিছু কঠিন নয়; বাহবিস্তু বলে জ্ঞানের কোনো বিষয় না। থাকলেও, জ্ঞান বা ধারণাই জ্ঞানের বিষয় হলেও, বিভিন্ন ধারণার মধ্যে পার্থক্য তো আছেই; সেই পার্থক্যর দরুনই বিভিন্ন জ্ঞান পরস্পর থেকে পৃথক। এবং বিভিন্ন ধারণার মধ্যে যে বৈচিত্ৰ্য, তার ব্যাখ্যা করবার জন্যে বাহবিস্তু ও বাহবিস্তুর বৈচিত্ৰ্যকে মানবার কোনো প্রয়োজন পড়ে না; বাসনা-বৈচিত্র্য দিয়েই তার যথেষ্ট ব্যাখ্যা হয়, এবং এই বাসনা জিনিসটা বাহ পদাৰ্থ নয়, মানসপদার্থই। বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বাসনা-বৈচিত্ৰ্য দিয়ে জ্ঞান-বৈচিত্ৰ্যকে ব্যাখ্যা করবার যে প্ৰচেষ্টা করেছেন, তা আমাদের প্রাচীন কালে অনেকটা দার্শনিক সহজ বুদ্ধির মতোই ছিলো, এবং অন্তত স্বপ্নাদির বেলায় এ-কথা যে অসম্ভব নয়, তার সপক্ষে নিশ্চয়ই আধুনিক মনস্তত্ত্বের দোহাই দেওয়া যায়।
বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধের বাকি যুক্তিগুলির কথা। আপাতত অপ্রাসঙ্গিক হবে। তাছাড়া উপরোক্ত যুক্তিই তার প্রধান যুক্তি, এবং বার্কলি প্ৰমুখ সমস্ত ভাববাদীর যুক্তির সারমর্ম এই একই কথা। এই যুক্তিকে খণ্ডন করতে হলে মাত্র দুটো পথে এগোনো সম্ভব। হয়। প্ৰমাণ করতে হবে যে, জ্ঞানের গণ্ডির মধ্যেই জ্ঞাননিরপেক্ষ বস্তুর সত্তাকে প্ৰমাণ করা যায়, আর না-হয় তো বলতে হবে, চেতনানিরপেক্ষ বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানের স্বাক্ষর না থাকলেও অন্য স্বাক্ষর আছে এবং সে স্বাক্ষর অবিসংবাদিত। প্ৰথম পথে এগোনো অসম্ভব, কেননা-এ পথ আত্মবিরোধের পথ। দ্বিতীয় পথে এগোতে গেলে বিশুদ্ধ তর্কের দাবি বা বিশুদ্ধ বুদ্ধিকে চরম বলে মানা যায় না, প্রয়োগের কথা তুলতে হয়। মূর প্রমুখ সাম্প্রতিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের পক্ষে সে-কথা তোলা কেন সম্ভবপর নয়, এ আলোচনা স্বতন্ত্র। মোটের উপর কথা হলো, তারা সে পথে এগোতে চাননি। চেতনার গণ্ডির মধ্যে থেকে, তর্কের দাবি দেখিয়ে, তঁরা ভাববাদকে খণ্ডন করতে চান।
মুর বলছেন, জ্ঞানের বিষয় এবং বিষয়ের জ্ঞান, এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ অস্বীকার করার উপরই ভাববাদের প্রকৃত ভিত, অথচ এই তফাতকে স্বীকার না করে উপায়ও নেই। চেতনার বিষয় এবং বিষয়ের চেতনা যদি বিভিন্ন না হতো, তাহলে বিভিন্ন জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য সম্ভবপর হতো না। ‘লাল-রঙ’ সম্বন্ধে জ্ঞান এবং “নীল রঙ” সম্বন্ধে জ্ঞান, দুয়ের মধ্যে পার্থক্য ঠিক কীসের? নিছক চেতনা হিসেবে উভয় জ্ঞানই অভিন্ন, ফলে ভেদ নিশ্চয়ই জ্ঞানের বিষয়ে।
ভাববাদী বলবেন, এই যুক্তি ছাড়া মুর-এর ভাববাদ খণ্ডনের বাকি সবটুকুই নিছক ঘোষণামাত্র, প্ৰমাণ নয়। এবং এই যুক্তি দিয়ে, শুধু এই যুক্তি দিয়ে, ভাববাদকে নিশ্চয়ই খণ্ডন করা যায় না। প্রথমত, চেতনার বিষয়কে বিষয়ের চেতনা থেকে স্বতন্ত্র করা হচ্ছে নেহাত অৰ্থপত্তি হিসাবে, এবং অর্থপত্তির মূল্য বড় জোর সম্ভাবনামূলক। অর্থাৎ, এই যুক্তি বড় জোর বস্তুর বা বিষয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের সম্ভাবনা প্ৰমাণ করছে, অস্তিত্ব নয়। তাছাড়া, আসল প্রশ্ন হলো, সম্ভাবনা হিসেবে যে-বিষয়কে প্ৰমাণ করা গেল, তার প্রকৃত স্বরূপ কী রকম? ভাববাদী নিশ্চয়ই এমন কথা বলবেন না যে, জ্ঞানের বিষয় বলে সত্যিই কিছু নেই; মূর যেন ভাববাদীর ঘাড়ে এই কথা অধ্যস্থ করে। তারপর এই কথাকে খণ্ডন করেছেন। ভাববাদী বলবেন, চেতনার বিষয় নিশ্চয়ই আছে, এবং সেই বিষয়ের দািকনই এক চেতনা অপর চেতনা থেকে ভিন্ন; কিন্তু এই বিষয় জড়বস্তু নয়, অন্তর্বস্তু মাত্র। এ বিষয় যে অন্তর্বস্তু, বহির্বস্তু নয়, তার প্রমাণ হিসেবে ভাববাদী বলবেন, নিছক বহির্বস্তুরূপে, চেতনার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কবিরহিত অবস্থায়, তাকে কখনও জানা যায়নি। অথচ নিছক অন্তর্বস্তুর বিভিন্নতার দরুন জ্ঞানের বিভিন্নতা যে সম্ভবপর, তার উদাহরণ হিসেবে প্ৰাচীন দার্শনিকদের গন্ধৰ্বনগর দর্শন থেকে শুরু করে আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদের ব্যাধিত অপচ্ছায়ার উল্লেখ করা যায়। তাই মূর-এর যুক্তি ভাববাদকে সত্যিই খণ্ডন করতে পারে না।
নব্যবস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীদের ভাববাদ খণ্ডনের বেলাতেও একই কথা। তঁদের যুক্তির জৌলুশ অনেক কম, কিন্তু মেজাজ অনেক বেশি চড়া। ভাববাদের মূলে অন্তত সাত-সাতটা অনুপপত্তি তারা আবিষ্কার করেছেন। তার মধ্যে তিনটি –অতিসারল্য, দার্শনিক দুরাশা এবং বেহিসেৰী ভাষা ব্যবহারের অপবাদকোন কোন বিশেষ ভাববাদীর বিরুদ্ধে নিয়োগযোগ্য হলেও ভাববাদ মাত্রের বিরুদ্ধেই এইগুলি যে প্ৰযোজ্য হবে, তার কোনো মানে নেই। জড়বাদী, অজ্ঞানবাদী, এমন-কী বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদী কোনো দার্শনিকের ব্যক্তিগত দুর্বলতা যদি থাকে, তাহলে এইসব অভিযোগ তাদের বিরুদ্ধেই প্ৰযোজ্য। অর্থাৎ এগুলি কোনো বিশেষ দার্শনিক মতবাদের অনুপপত্তি নয়, কোনো কোনো দার্শনিক বিশেষের ব্যক্তিগত দুর্বলতামাত্র। তাই এগুলিকে বাদ দিতে হবে। নিছক দার্শনিক মতবাদ হিসেবে ভাববাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ চারটি; এবং মজার কথা এই যে, সে চারটি অভিযোগের নামরূপে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন, সবগুলির মূলেই বক্তব্য এক।
(১) এ পর্যন্ত মানুষ যা জেনেছে, তা সমস্তই জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল বলে সমস্ত বস্তুই যে জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য, এমন কোনো কথা নেই; (২) জ্ঞানের সময় চেতনার সঙ্গে বিষয়ের সম্পর্ক আছে বলে সে সম্পর্ক যে ত্ৰৈকালিক হতে বাধ্য, এমন কোনো কথা নেই,-যে লোক আজ রিপাবলিকান রাজনীতি করছে, আগামীকাল সে যে ডিমোক্রাটুদের ডেরায় ভিড়বে না, এমন কথা কি কেউ জোর করে বলতে পারে? (৩) বিষয়ের প্ৰাথমিক পরিচয়ে চেতনা-নির্ভরতা থাকলে এই পরিচয় যে তার চিরন্তন পরিচয় হবে, এমন কোনো কথা নেই,–“আগল” “পাগল” “ছাগল” শব্দে “গ” অক্ষর দ্বিতীয় অক্ষর বলে “গ” যে সর্বদাই শব্দের দ্বিতীয় অক্ষর হবে একথা দাবি করা যায় কি? (৪) বিষয়ের পক্ষে জ্ঞাত হওয়া গৌণ লক্ষণ মাত্র, তাকে মুখ্য লক্ষণ মনে করলে চলবে না, – প্রেমিকের সত্তা প্রেমের উপর নির্ভর করে নিশ্চয়ই।
রাজনীতি থেকে শুরু করে হৃদয়ঘটিত ব্যাপার পর্যন্ত রকমারি দৃষ্টান্ত! একের পর এক অকাট্য যুক্তি। একের পিঠে শূন্য বসালেও দশ হয়, দশের পিঠে শূন্য বসালেও একশো হয়—একটি যুক্তির উপর আর একটি যুক্তি চাপিয়ে খণ্ডন করলে খণ্ডনের গুরুত্ব এইরকম হুড়হুড় করে বেড়ে যেতে পারে, অনুবতী যুক্তি যতই দুর্বল হোক না কেন। কিন্তু শূন্যের পিঠে যাই বসানো যাক, ফল শুধুই শূন্যই, গুরুত্ব এতটুকুও বাড়ে না। নব্যবস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীর প্রথম বা একটি যুক্তির মূল্যও যদি শূন্যর চেয়ে বেশি হতো, তাহলে সত্যিইভাবনা থাকত না, ভাববাদকে যুক্তি দিয়ে ভেঙেচুরে মিসমার করে দেওয়া যেত। কিন্তু ভাববাদের খণ্ডন হিসেবে কোনো একটি যুক্তিও শূন্যর চেয়ে বেশি সারবান নয়। তাই সাত-সাতটা যুক্তির পরেও ফল দাঁড়িয়েছে শুধু শূন্য দিয়ে শূন্যকে গুণ করার মতো।
ভাববাদী বলবেন, শুধুমাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্তে জ্ঞানের উপর বিষয়কে নির্ভরশীল হতে দেখে আমি যদি বলতুম, জ্ঞানের উপর বিষয় একান্তভাবে নির্ভর করে, তাহলে আমার কথাকে খণ্ডন করবার জন্যে নব্যবস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদীর পক্ষে অত বড় অনুপপত্তির ফর্দ দরকার পড়ত না। কিন্তু আসল কথা মোটেই তা নয়। আসল কথা হলো-এমন কোনো বিষয়ের সন্ধানও মানুষ এখন পায়নি, যার সত্তা চেতনানিরপেক্ষ। অতীতের সমস্ত মানুষ এবং বর্তমানের সমস্ত মানুষ দাড়কাককে কালো বলে চিনেছে বলেই দাঁড়কাকমাত্ৰকেই কি কালো বলে মানার তাগিদ নেই? অবশ্য, শুধু এ জাতীয় যুক্তি-স্বদেশী ন্যায়শাস্ত্রে যাকে বলে অন্বয় – সুনিশ্চিত নিগমন স্থাপন করতে পারে না, শুধু অবাধিত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে যে নিগমন পাওয়া যায়, তা সম্ভাবনামূলক মাত্র। কেননা, এখানে বিপরীত অভিজ্ঞতার কথা অন্তত কল্পনা তো করা যায়-বিপরীত অভিজ্ঞতা এতদিন পর্যন্ত অবাস্তব হলেও অসম্ভব। মোটেই নয়। কিন্তু ভাববাদী বলবেন, আমার দর্শনের ভিত্তি এত কঁাচা নয়, অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ বিষয়কে এতদিন যে অভিজ্ঞতার মধ্যে পাওয়া যায়নি। শুধু তাই নয়, তাকে পাবার কথা ভাবাই যায় না, এমন-কী কল্পনাতেও নয়। কেননা, নিছক বিষয় বা বিষয়মাত্রকে পাবার কথা কল্পনা করতে গেলে অন্তত কল্পনার সঙ্গে তার সম্পর্ক স্বীকার করতে হবে; এবং কল্পনা যে-হেতু মানসক্রিয়ার প্রকারমাত্র, সেইহেতু উক্ত বিষয়কে মানসক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত, অতএব মানসক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল, মনে না করে উপায় নেই। তাই মানস-নিরপেক্ষ বিষয়ের কথা সোনার পাথরবাটির মতো। সোনার পাহাড় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা না হলেও তার অস্তিত্ব কল্পনায় স্ববিরোধ নেই, কিন্তু সোনার পাথরবার্টির শুধু অভিজ্ঞতা অসম্ভব নয়, তার অস্তিত্ব-কল্পনায় স্ববিরোধ। অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ বিষয়ের কথাও ওইরকমই স্ববিরোধী–কেননা, বিষয় মানেই অভিজ্ঞতার বিষয়, তা সে বাস্তব অভিজ্ঞতাই হোক, আর কাল্পনিক বা সম্ভব অভিজ্ঞতাই হোক।
মূর একদা বলেছিলেন, ভাববাদীর মতে যে-হেতু অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ বস্তুর সত্তা থাকতে পারে না, সেইহেতু মানতে হবে, ট্রেন একবার প্লাটফর্ম ছাড়বার পরই তার চাকা উবে যায়, কেননা চলন্ত ট্রেনে বসে ট্রেনের চাকা তো চোখে দেখা যায় না। কিন্তু এই বিদ্রুপের ভাববাদী জবাব অতি সরল; চলন্ত ট্রেনের চাকাকে অযথার্থ মনে করা ভুল হবে, কেননা তা অভিজ্ঞতারই বিষয়; কেবল এই অভিজ্ঞতা বাস্তব অভিজ্ঞতা নয়, “সম্ভব”। অভিজ্ঞতা মাত্র। “যে টেবিলের উপর আমি এখন লিখছি”, বার্কলি বলেছিলেন, “সে টেবিলের অস্তিত্ব আছে; অর্থাৎ আমি একে দেখতে পাই, অনুভব করতে পারি; এবং আমি যদি পড়ার ঘরের বাইরে যৌতুম, তাহলেও আমি বলতুম, এর অস্তিত্ব আছে; অর্থাৎ পড়ার ঘরে থাকলে আমি তাকে অনুভব করতে পারতুম; কিংবা অন্য কোন আত্মা বাস্তবিকই তাকে অনুভব করছে।”
সাম্প্রতিক বস্তম্বাতন্ত্র্যবাদীর ভাববাদ খণ্ডন যে কীরকম পঙ্গু ও অথর্ব, আর একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়ে এ আলোচনা শেষ করব। আলেকজাণ্ডার হলেন সাম্প্রতিক বস্তুস্বাতন্ত্র্যবাদের আর একজন দিকপাল দার্শনিক। বিশ্বের সমস্ত সত্তাকে তিনি দুভাগে ভাগ করেছেন, মন আর বহির্বস্তু। এক ভাগের একটির সঙ্গে অপর ভাগের আর একটির সংযোগ ঘটলে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার জন্ম হয়। ভেবে দেখতে হবে, এই সংযোগঠিক কোন জাতের। আলেকজাণ্ডার বলেন, এই সংযোগ-বিচারে ভাববাদীর দল মনকে অযথা প্ৰাধান্য দিয়ে বসে, মনে করে, এই সংযোগের ক্ষেত্রে জ্ঞানের বিষয় নির্ভর করে জ্ঞানের উপর। আসলে কিন্তু মোটেই তা নয়, এ সংযোগ অতি সাধারণ একত্র-সমাবেশ মাত্র, যে রকম একত্ৰসমাবেশ ডিশের সঙ্গে টেবিলের ৭ ডিশের উপর টেবিলের সত্তা নির্ভর করে। না, টেবিলের উপর ডিশের সত্তাও নয়। মনের উপর বিষয়ের সত্তা নির্ভর করবে। কেন? কিন্তু শুধু এই কথা বলে থেমে যাওয়া যায় না, জ্ঞান নামক একত্র-সমাবেশের অন্তত একটা কোনো বৈশিষ্ট্য তো মানতেই হয়, কেননা যে-কোনো একত্ৰ-সমাবেশের বেলায় তো জ্ঞান হয় না! আলোকজাণ্ডার বলছেন, এ বৈশিষ্ট্য সমাবেশের বৈশিষ্ট্য নয়, সমাধিত এক উপাদানের বৈশিষ্টা মাত্র। অর্থাৎ অন্যান্য সমাবেশের বেলায় উভয় উপাদানই বহির্বস্তু, জ্ঞানের বেলায় একটি উপাদান হলো মন বা জ্ঞাতা। এই কথা শুনে ভাববাদী নিশ্চয়ই বিক্রম করে বলতে পারেন–অর্থাৎ আলেকজাণ্ডারের মতে “জ্ঞান” হলো এমন এক একত্ৰ-সমাবেশ, যার একটি উপাদানের মধ্যে “জ্ঞান” বর্তমান; এবং ন্যায়শাস্ত্রের অতি সাধারণ ছাত্রও জানে, এই জাতীয় সংজ্ঞা petitio principii নামের এক সরল অনুপপত্তি।
০৩. বুদ্ধি দিয়ে, তর্ক করে, ভাববাদকে খণ্ডন করা যায় না
বুদ্ধি দিয়ে, তর্ক করে, ভাববাদকে খণ্ডন করা যায় না; এ প্রচেষ্টা স্বয়ংবিরুদ্ধ, আত্মঘাতী। কেননা, এই পথে এগুতে গেলে বুদ্ধির দাবিকে, চেতনার দাবিকেই চরম দাবি বলে মেনে নিতে হয়,–আর সেটিকুই তো ভাববাদের আসল কথা। তাই, দিকপাল দার্শনিকও ভাববাদকেই খণ্ডন করতে এগিয়ে শেষ পর্যন্ত ভাববাদের জালেই জড়িয়ে পড়েছেন-দর্শনের ইতিহাসে এ যেন এক গোলকধাঁধাই। যুগে যুগে বারবার মানুষের চরম বুদ্ধি, চরম মনন-মনীষা ভাববাদকে অসম্ভব বলে চিনতে চেয়েছে, তবুও মুক্তি পায়নি তার সম্মোহিনী দাসত্ব থেকে। যেন মৃত্যুর পরই পৌরাণিক দেবতার পুনরুজ্জীবন, আর দর্শনের মন্দিরে আপাত তেত্রিশকোটি দেব-দেবীর মধ্যে এই দেবতার উদ্দেশ্যেই প্ৰায় তৈলধারার মতো অবিচ্ছিন্ন উপাসনা।
ভাববাদী তো উল্লাস করে বলবেনই; ভাববাদ খণ্ডনের সমস্ত প্ৰচেষ্টাই বৃথা। এ যেন ভাইয়ে-ভাইয়ে মামলাবাজি (কেয়ার্ড), কেননা দর্শন আর ভাববাদ নেহাতই তো সহোদর। কিংবা, যা একই কথা, যা কিছু বুদ্ধিসহ, তাকেই যথাৰ্থ বলে মানতে হবে, আবার যা কিছু যথার্থ, তাকেই বুদ্ধিসহ বলতে হবে (হেগেল)। সত্তা আর চেতনা যেন একই কাচের উত্তল আর অবতল দুটো দিক, যেন একই চুম্বকের দুই মেরুকেন্দ্র। একটিকে বাদ দিয়ে আর একটির কথা ভাবাই যায় না, যেমন ভাবা যায় না। একটা ছড়ির কথা, যে-ছড়ির মাত্র একটি প্রান্ত! দর্শন যদি সত্তা-সন্ধানী হয়, এবং সত্তার রূপ যদি আনিবাৰ্যভাবেই চেতন-নির্ভর হয়, তাহলে ভাববাদ ছাড়া দর্শনের পক্ষে আর কী গতি হতে পারে? ভাববাদ সমস্ত দর্শনেরই যে আনিবাৰ্য পরিণাম শুধু তাই নয়, দার্শনিক প্রচেষ্টারই নামান্তরমাত্র।
হেগেল-কেয়ার্ড-এর এই যে কথা, একদিক থেকে দর্শনের অতীত ইতিহাসের এমন নিখুঁত বর্ণনা একান্তই বিরল। আবার অন্যদিক থেকে, অসত্যের এমন চূড়ান্ত দৃষ্টান্তও দুর্লভ কম নয়।
দর্শনের অতীত ইতিহাসটুকুর আশ্চৰ্য নিখুঁত বৰ্ণনা। কেননা যাকে আমরা এতদিন ধরে দর্শন বলে জেনেছি, তার চূড়ান্ত আবেদন শেষ পৰ্যন্ত বিশুদ্ধ চেতনার কাছেই–তৰ্কশাস্ত্রের হাজার রকম জটিল আলিগলি ঘুরে বিশুদ্ধ বুদ্ধির আর বিচারের দাবি অনুসারেই দার্শনিক আলোচনার শেষ সিদ্ধান্ত সন্ধান করা হয়েছে। এক কথায়, চেতনাকেই মেনে নেওয়া হয়েছে দর্শনের চরম কষ্টিপাথর বলে।
অবশ্য তাই বলে বিপরীত মতবাদ–অচেতনকারণবাদ বা বস্তুবাদ—মাঝে মাঝে মাথা তোলবার চেষ্টা যে করেনি, তা নয়। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত–অর্থাৎ আধুনিক যুগে আধুনিক বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠা হবার আগে পর্যন্ত–তার পরমায়ু নেহাতই ক্ষীণ, তার পদক্ষেপ দ্বিধাবিড়ম্বিত, আত্মনিশ্চয়তার অভাবে সে এগিয়েছে আত্মঘাতের পথে, এমন-কী বিরুদ্ধ আবহাওয়ায় পড়ে সে অনেক সময় একটা রফা করে নিতে চেয়েছে বিরুদ্ধ মতবাদের সঙ্গেই-চেতনকারণবাদের সঙ্গেই। এই বস্তুবাদ সম্বন্ধে সাধারণ দার্শনিক সমাজের ভঙ্গিটাও লক্ষ করবার মতো; সাদর সম্ভাষণ তার কপালে কোনোদিনই জোটেনি, বরং জুটেছে শুধু প্ৰতিবন্ধ আর বিড়ম্বনা। যখন সে দুঃসাহসীর মতো বড় বেশি দুবিনীত হইচই শুরু করেছে, তখন তাকে দর্শনের আঙিনার এক কোনায় বড়জোর একটুখানি আসন করে দেওয়া হয়েছে অম্পশ্যের মতো, কিন্তু সেই সঙ্গেই চক্রান্ত-পরামর্শ চলেছে, কেমন করে তাকে একেবারে একঘরে করে তার ভিটেমাটি পর্যন্ত উচ্ছেদ করা যায়। কখনো বা তাকে খোলাখুলি গালাগালি করে একেবারে উচ্ছন্নে পাঠাবার ব্যবস্থা, কখনো বা তাকে সংস্কার করে জাতে তুলে নেবার অজুহাতে একেবারে সর্বস্বাস্ত করে দেবার কৌশল। খোলাখুলি গালাগালি করবার দৃষ্টান্ত সংখ্যায় বহুলতর, এমন-কী অনেকসময় ‘বস্তুবাদ’ শব্দটি দার্শনিক অপচেষ্টার নামান্তর হিসেবে ব্যবহৃত। কিন্তু এ জাতীয় দৃষ্টান্ত অনেক স্থূল, অনেক ভোতা। এর মধ্যে চিত্তাকর্ষণ কম। বরং, সংস্কার করবার নামে সর্বস্বাস্ত করবার উদ্যম দৃষ্টান্ত হিসেবে অনেক বেশি চিত্তাকর্ষক। এ-উদ্যমের উদাহরণ সর্বদেশে, সর্বযুগে; অতীতের ভারতবর্ষে, প্ৰাচীন গ্রীসে, আধুনিক ও সাম্প্রতিক য়ুরোপে-প্ৰায় সর্বত্রই। আমাদের দেশে চার্বাকের দেহাত্মবাদ দেবগুরু বৃহস্পতির কৃটি অভিসন্ধি বলে প্রচারিত; সাংখ্য দর্শনের মধ্যে প্ৰধানকারণবাদের রেশটুকুকে সংস্কার করতে করতে শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানভিক্ষু এর মধ্যে এমন-কী ঈশ্বরের জন্যও জায়গা করে ফেললেন; বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের পর বৈভাসিক ও সৌত্ৰিাস্তিকদের মধ্যে বস্তুবাদের যতটুকু ভগ্নাংশ পড়েছিল, সেটুকুকে উপহাস করে মাধ্যমিক আর যোগাচাররা প্রচার করলেন-তথ্যাগতের পক্ষে ওটুকু নেহাতই মন্দবুদ্ধির মানুষকে প্ৰবোধ দেবার প্ৰচেষ্টা। বিদেশের দর্শনেও একই কথা। গ্ৰীক যুগে ডিমক্রিটাস-কে সংস্কার করলেন এ্যানেক্সাগোরাস, আবার এ্যানেক্সাগোরাস-কে সোফিস্ট, আর সোফিস্টদের সংস্কার করলেন সক্রেটস-দুৰ্জয় বস্তুবাদ থেকে চেতনকারণবাদে পৌছবার যেন সোজা-সড়ক বেরিয়ে গেল। আধুনিক ইংলণ্ডেও এ উদাহরণের ব্যতিক্রম নেই।–বেকনা-হবাস-এর বস্তুবাদকে শুধরে নিলেন লক, আবার লককে শুধরে নিলেন বার্কলি-হিউম, শোধরানোর মানে দাড়ালো বস্তুবাদের শবদেহের উপর ভাববাদী প্রেতসাধনা। আবার এদিকে দেকার্ত, বস্তুবাদের সঙ্গে তিনি আপাস করেছেন। দ্বিধাভারা ভাববাদের। দেকার্ত-এর পর পিনোজা, দি তবুও পরমার্থিক ভাববাদের মধ্যে ব্যবহারিক বস্তুবাদকে ঠাই দিয়েছেন। (“পিটারের মন পিটারের দেহ” ইত্যাদি); আর তারপর লাইবনিৎস, বস্তুবাদের ক্ষীণতম স্বাক্ষরটুকুও তিনি লোপ করে দিলেন, জড় হল চিৎপরমাণুর প্ৰতিভাস-মাত্রে।
এতদিন পর্যন্ত সবদেশে সব যুগে এই একই কথা; বস্তুবাদের কপালে যদিই বা কখনো সাময়িক সাফল্য জুটেছে (যেমনটা দেখা যায় ফরাসী বিপ্লবের অগ্রদূত ফরাসী বস্তুবাদের বেলায়), তবুও সেই সাফল্যের পরই বিদগ্ধ সমাজ হয় একে একেবারে সোজাসুজি উড়িয়ে দিতে চেয়েছে, আর না হয়। তো সংস্কার কয়ে নেবার নামে একেবারে সর্বস্বাস্ত করে ছেড়েছে। যে-সৰ দিকপাল দার্শনিক ভাববাদের অসম্ভবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন, তাঁরাও কেউ বিপরীত মতবাদ–বস্তুবাদের–দিকে অগ্রসর হতে পারেননি, ভাববাদকে ছেড়ে আর এক অভিনব দার্শনিক মতবাদ সন্ধান করতে বেরিয়েছেন, আর শেষ পর্যন্ত এই অভিনব মতবাদের দোহাই দিয়ে প্রচ্ছন্ন ভাববাদের আঙিনাতেই ক্লান্ত দার্শনিক চেতনা এলিয়ে দিয়েছেন। ফলে দর্শনের ইতিহাসে চেতন-কারণবাদেরই অবিচ্ছিন্ন প্ৰতিপত্তি, দর্শন আর ভাববাদ যেন একই কাচের উত্তল আর অবতল দুটো দিকমাত্ৰ!
প্রশ্ন হলো : দর্শনের ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটল কেন? দর্শন কেন মুক্তি পায়নি ভাববাদের প্রায় একচ্ছত্র আধিপত্য থেকে? চেতনকারণবাদেই কেন তার একান্ত পরিণতি? তথাকথিত বিশুদ্ধ দর্শনের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চাইলে এ-প্রশ্নের জবাব খোজা বিফল হবে। বড় জোর, শুধু এইটুকু বলা চলবে যে, এতদিন পর্যন্ত বুদ্ধির দাবিকে বা চেতনার দাবিকে (তথাকথিত বুদ্ধিবিতৃষ্ণ দার্শনিকরাও বুদ্ধিকে বাদ দিয়ে চেতনারই অপর কোন অঙ্গকে আশ্রয় করতে চেয়েছেন)। চরম দার্শনিক পদ্ধতি বলে মেনে নেবার দরুন দর্শনে এমনটা না হয়ে আর উপায় ছিল না! অথচ, পদ্ধতির দিক থেকে চেতনার উপর নির্ভর করা, আর পরিণামের দিক থেকে ভাববাদ-এ তো একই কথার ভিন্ন প্ৰকাশভঙ্গিমাত্র। কেন এমন হয়েছে? তাই আসল সমস্যাটা আরো অনেকখানি গোড়ার সমস্যা। সে-সমস্যা হলো : যুগ যুগ ধরে দার্শনিকেরা কেন চেতনার দাবিকে চূড়ান্ত দাবি বলে প্রচার করেছেন, কিংবা, যা একই কথা, পরমসত্তাকে চেতননির্ভর না বলে কেন শেষ পর্যন্ত শান্তি পাননি?
“বিশুদ্ধ” দর্শন এই “কেন’-র জবাব জোগাতে পারে না। অথচ মানবসমাজের ক্রমবিকাশের সঙ্গে মানব-চেতনায় দার্শনিক মতবাদের ক্রমবিকাশের কথাটা যদি মিলিয়ে ভাববার চেষ্টা করা যায়, তাহলে সেদিক থেকে এই প্রশ্নের জবাবটা স্পষ্ট : এতদিন ধরে এমনিতরো ঘটনা না ঘটে যেন উপায়ই ছিল না! কেননা যাকে আমরা “দর্শন” বলে মেনেছি, তার জন্ম শ্রেণীবিভক্ত সমাজের গর্ভে, সে লালিত হয়েছে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ক্ৰোড়ে, তার দেহ থেকে শ্ৰেণীবিভাগের চিহ্ন মোছা যাবে কেমন করে? ভাববাদ বা চেতন-কারণবাদ–সেই শ্রেণীবিভাগের চিহ্ন! সমাজে শ্রেণীবিভাগকে উচ্ছেদ না করলে তাই ভাববাদের হাত থেকে প্রকৃত মুক্তি পাবার প্রশ্ন ওঠে না; মার্কস বলছেন, দার্শনিকেরা এতদিন দুনিয়ার শুধু ব্যাখ্যাই খুঁজেছে, কিন্তু আসল কথা হলো দুনিয়াকে বদল করবার কথা। দুনিয়াকে বদল করা-পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী, নবীন নিঃশ্ৰেণীক সমাজ। তখন মানুষের সঙ্গে সংগ্রামে মানুষ আর নিজেকে অপচয় করবে না, তখন থেকেই যেন মানুষের আসল ইতিহাস শুরু। প্ৰাক্-ইতিহাস শেষ, শুরু ইতিহাস। আর শেষ ভাববাদের। সোভিয়েট দেশে এই নবীন নিঃশ্ৰেণীক সমাজের প্রথম অঙ্কুর, তাই ভাববাদের হাত থেকে মুক্তি, বস্তুবাদের প্রথম বলিষ্ঠ প্ৰতিষ্ঠা।
বিশুদ্ধ দার্শনিক প্ৰত্যেকটি কথাতেই বিরূপ হবেন। না-হলেই বরং অবাক হবার কথা, কেননা তার চেতনাও যে এই শ্রেণীবিভক্ত সমাজেরই পরিণাম, তাই শ্রেণীবিভক্ত সমাজেরই মুখপাত্র দার্শনিক বিচার যদি সমাজ-বিপ্লবের প্ৰসঙ্গ তোলে, তাহলে তাঁর পক্ষে বিরূপবোধই স্বাভাবিক বইকী! মার্কসীয় দর্শনের বিরুদ্ধে আজকের দিনে কেন যে এত রকম অভিনব প্ৰতিবন্ধ, তার ব্যাখ্যাও এদিক থেকে খুঁজে পাওয়া যাবে।
আপাতত দেখা যাক, সমাজে শ্রেণীবিভাগের সঙ্গে দর্শনের ক্ষেত্রে ভাববাদের সম্বন্ধটা কী-রকম।
শ্ৰেণীবিভক্ত সমাজের গর্ভে দর্শনের জন্ম, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ক্ৰোড়ে। দর্শন লালিত, দর্শনের দেহে তাই শ্রেণীবিভাগের চিহ্ন। কিন্তু তার আগে? তার আগে মানবসমাজ শ্রেণীবিভক্ত ছিল না, আর তাই মানুষের চেতনা ভাববাদের আশ্রয় খুজতে বাধ্য হয়নি। আর এর পর? এর পর এক নবীন নিয়শ্রেণীক সমাজে-সে-সমাজে ভাববাদের বীজও বিলুপ্ত-এই বীজ থেকে উৎপন্ন বিষবৃক্ষ শুধু জীৰ্ণ শুষ্ক কাষ্ঠের মতো সংস্কৃতির জাদুঘরে গবেষকের কাছে ঐতিহাসিক বিস্ময়ের বিষয়মাত্র। পরমায়ুর দিক থেকে তাই শ্রেণী:সমাজ আর ভাববাদ সমব্যাপ্ত-কিংবা যেন একই কাচের উত্তল আর অবতল দুটো দিক।
আগে ছিল আদিম-সাম্যাবস্থা। মানুষের সংস্কৃতির সবটুকুকে তখন জুড়ে ছিল তার নাচ আর তার ইন্দ্রজাল,–কিংবা নাচে-ইন্দ্ৰজালে মেশা এক প্ৰাগবিভক্তি সাংস্কৃতিক সত্তা। এই যে প্ৰাথমিক প্ৰাগবিভক্তি সংস্কৃতি, এর স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে, এর মূল দাবি ভাববাদের বিপরীত দাবি। আলোচনা করতে হবে, কেমন করে আদিম সাম্যাবস্থা-বিচ্যুতির পর –মানবসমাজে শ্রেণীবিভাগ দেখা দেবার পর -এই প্ৰাথমিক প্ৰাগবিভক্ত ভাববাদ-বিরুদ্ধ সংস্কৃতি থেকে ভাববাদী দর্শন (প্ৰথমে ধর্ম, আর তারপর ধর্মেরই পরিচ্ছন্ন সংস্করণ দর্শন বা অধিবিদ্যা) তত্ত্বান্বেষণের সমস্তটুকুকে জুড়ে বসতে লাগল। অবশ্যই শ্রেণীবিভক্ত সমাজেরও ইতিহাস আছে, শ্রেণীবিভাগের কাঠামোর মধ্যেও অনেক রকম পরিবর্তন ঘটেছে; তাই দর্শনের বা ভাববাদের চেহারাও যুগে যুগে এক নয়। আরো দেখতে হবে, শ্রেণীবিভাগের এই কাঠামো সত্ত্বেও মাঝে মাঝে বস্তুবাদ কেমন করে মাথা তুলে দাড়াবার চেষ্টা করছে। যেমন ধরা যায়, ফরাসী বস্তুবাদ, বা আধুনিক ইংরেজী বস্তুবাদ। তার আবির্ভাব তো শ্রেণীসমাজের যুগেই। শ্রেণীসমাজের মূলেই যদি ভাববাদী দর্শনের অনিবাৰ্য তাগিদ থাকে, তাহলে এমন ঘটনা সম্ভব হয় কেমন করে? অবশ্যই, ও-জাতীয় বস্তুবাদের দুর্বলতা ছিল। সেই দুর্বলতার দরুনই এই বস্তুবাদ বাধ্য হলো ভাববাদের জন্যে জায়গা ছেড়ে দিতে। তারপর আধুনিক যুগে সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনার আবহাওয়ায়, সোভিয়েট সমাজে মানবইতিহাসে প্রথম পবিপূর্ণভাবে ভাববাদ অগ্ৰাহ করবার-সচেতন আর সমবেতভাবে অগ্রাহ করবার-উৎসাহ দেখা দিল। এ-উৎসাহের উৎসই বা কোথায়? এ সব প্রশ্নের জবাব থেকে ভাববাদ খণ্ডনের মূল রহস্য আবিষ্কার করবার আশা আছে।
আদিম সাম্যাবস্থার প্রাগবিভক্তি সংস্কৃতির প্রধান অভিব্যক্তি ইন্দ্ৰজাল। ইন্দ্ৰজালের প্রধান বিকাশ নাচের মধ্যে। নাচ, কিন্তু আমরা যে অবসর-বিনোদনকে নাচ বলতে অভ্যন্ত, তা নয়। নাচ বলতে চোদ্দ আনাই ইন্দ্ৰজাল। এই ইন্দ্ৰজাল সম্বন্ধে সভ্য মানুষের ভ্ৰান্তির অন্ত নেই। নাচ, কিন্তু আজকালকার অবসর-বিনোদন নয়। আদিম মানুষের কাছে বিনোদিত হবার মতো অবসর কোথায়? চার পা ছেড়ে সবে সে দু’পায়ে উঠে দাড়াতে শিখছে, আর শিখেছে আগেকার দুটো ফালতু পা-কে দু হাত হিসেবে ব্যবহার করতে। হাতিয়ার তৈরি করতে শিখল, তাই হাত। দুনিয়ার আর কোনো জানোয়ার হাতিয়ার বানাতে শেখেনি, ‘হাত” নেই। আর কারুর। হাতের সঙ্গে মগজের যোগাযোগ, তাই হাতিয়ার ব্যবহারের মাধ্যমেই বুদ্ধিরও ক্ৰমবিকাশ। কিন্তু আদিম মানুষের প্রথম সেই হাতিয়ার বড় স্থূল, প্ৰকৃতিকে জয় করবার কাজে প্ৰায় অকৰ্মণ্যের চেয়ে মাত্র একটুখানি বেশি। সামনে প্ৰকৃতি, বিরাট বিপুল প্ৰকৃতি -থুল আর প্রাকৃত ওই হাতিয়ার নিয়ে মানুষ এই প্ৰকৃতিকে যতটুকু জয় করতে পেরেছে, ততটুকুই তার দুঃখ-মুক্তি। প্ৰকৃতির সঙ্গে লড়াই, হাতে মাত্র সামান্য হাতিয়ার। কতটুকুই বা পেরে ওঠা যায়? তবু যেটা সবচেয়ে জরুরি কথা, হাতিয়ার হাতে প্ৰকৃতিকে জয় করতে নেমেছিল বলেই মানুষ প্ৰকৃতিকে চিনতে শুরু করল, আর চিনতে শিখাল যত ভালো করে, ততই ভালো করে। পারল জয় করতে। জ্ঞান এসেছে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে, আবার জ্ঞান হয়েছে সংগ্রামের অন্ত্র, তাই সংগ্রামকে বাদ দিয়ে নিছক তত্ত্বজিজ্ঞাসার কথা আদিম মানুষের বেলায় ওঠেই না। কেবল মনে রাখতে হবে, এ সংগ্রাম মানুষের সঙ্গে প্ৰকৃতির, মানুষের সঙ্গে মানুষের নয়। কেননা, তখন ছিল আদিম সাম্যাবস্থা, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কটা সমাজ-সহজ সম্পর্ক। শোষণ নেই, তাই শাসনও নেই। শোষণ থাকবে কেমন করে? হাতিয়ার তখন অতি স্থূল বলেই দলের সবাই মিলে প্ৰাণপাত পরিশ্রম করে পৃথিবীর কাছ থেকে যেটুকু জিনিস সংগ্ৰহ করতে পারে, তার সাহায্যে কোনমতে দলের সবাইকার মাত্র জীবনধারণটুকু সম্ভব। তাই কারুর পক্ষেই অপরের শ্রম দিয়ে গড়া জিনিস আত্মসাৎ করতে পারা সম্ভব নয়। অর্থাৎ কিনা সম্ভব নয় শোষণ। আর শোষণ সম্ভব নয় বলেই সম্পর্কটা হলো সমানে সমান। সাম্যসমাজ। যদিও কিনা আদিম। সকলেই সমান, কেননা সকলেই সমান গরিব হতে বাধ্য। তবুও, এই সাম্যজীবনে একের সঙ্গে দশের সম্পৰ্কটা যেন অঙ্গাঙ্গী। সমাজ তখন বিশিষ্ট মানুষের সমষ্টিমাত্র নয়, যেন এক অখণ্ড সমগ্ৰতা; একের সঙ্গে দশের সম্পর্ক সংখ্যাগণিতের সম্পর্ক নয়, অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। তাই, মানুষের সংগ্ৰাম আর জান, কিংবা সংগ্রাম-জ্ঞানের সেই প্ৰাগবিভক্ত সত্তায়, সমগ্রতার চেতনা প্ৰতিফলিত-ব্যষ্টির চেতনা নয়, শ্রেণীর চেতনা নয়, সমগ্ৰ সমাজের প্রাগবিভক্ত চেতনা। এই চেতনা আদিম মানুষের গোষ্ঠী নৃত্যে, — গোষ্ঠী-নৃত্য গোষ্ঠী-জীবনের অঙ্গমাত্র। সে-নাচের মধ্যেই আদিম মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন, কিন্তু সে সংস্কৃতিতে অবসর বিনোদনের উৎসাহ নেই, নেই বিশুদ্ধ তত্ত্ব অন্বেষণের তাগিদ। তার বদলে সোজাসুজি প্ৰকৃতিকে জয় করবারই তাগিদ। কিন্তু জয়োৎসাহের বাস্তব সম্ভাবনাটা নেহাতই সংকীর্ণহাতিয়ার যে তখন নেহাতই স্থূল ধরনের। তাই প্ৰকৃতিকে জয় করবার বাস্তব বিফলতাকে কল্পনার জয় দিয়ে, বা জয়ের কল্পনা দিয়ে পূরণ করে নেবার চেষ্টা। তারই নাম ইন্দ্ৰজাল। ইন্দ্ৰজাল মানে হলো, প্ৰকৃতিকে যে-কাজ করবার জন্যে বাধ্য করতে চাই, নিজেরাই সে-কাজের একটা নকল করা, আর মনে মনে কল্পনা করা যে, প্ৰকৃতি এই নকলটাকেই নকল কয়তে বাধ্য হবে।–অর্থাৎ কিনা আসল ঘটনাটা ঘটতে বাধ্য হবে প্ৰকৃতিতে। আকাশে হয়তো বৃষ্টির নকল তুললাম আর ভাবলাম সত্যিই বৃষ্টি হবে।
শ্ৰীমতী হারিসন দেখাচ্ছেন :
অসভ্য মানুষ হলো কাজের মানুষ। তার নিজের মনে যে-কাজ করবার ইচ্ছে, সে-কাজ করবার জন্যে কোনো দেবতাকে অনুরোধ করবার বদলে সে নিজেই কাজটা সারবার চেষ্টা করে। প্ৰাৰ্থনার বদলে সে উচ্চারণ করে মন্ত্র। এক কথায়, সে ইন্দ্ৰজাল ব্যবহার করে, আর প্রায়ই সে মেতে ওঠে। ঐন্দ্ৰজালিক নাচে। রোদ বা হাওয়া বা বৃষ্টি চাইলে সে গির্জায় গিয়ে কোনো অলীক দেবতার সামনে নুয়ে পড়ে না, নিজের গোষ্ঠীকে আহবান জানায়-আর তারপর সকলে মিলে একসঙ্গে রোদের নাচ বা হাওয়ার নাচ বা বৃষ্টির নাচ নাচতে শুরু করে। ভালুক শিকার বা ভালুক ধরবার আগে সে ভালুককে বশ করবার মতো শক্তি পাবার আশায় তার দেবতার পায়ে মাথা কোটে না, শিকারের মহড়া দেয় ভালুক-নাচ নেচে। আবার :
গ্রীকরা বুঝেছিল, আপনি যদি মন্ত্রাচরণ করতে চান, তাহলে কিছু কাজ করা দরকার; অর্থাৎ ‘আপনার মধ্যে শুধু কিছু ভাবাবেগ জাগলে চলবে না, তাকে কাজের রূপে প্ৰকাশ করতে হবে।’ তাছাড়া ‘মন্ত্রাচরণের একটি অঙ্গকে আমরা আগেই পরীক্ষা করেছি, সেই অঙ্গ হলো মন্ত্রাচরণ সমবেতভাবে করা দরকার, অনেকগুলি মানুষের পক্ষে এক সঙ্গে একই আবেগ অনুভব করা দরকার।’ ইত্যাদি ইত্যাদি।
এই তো গেল আদিম মানুষের নাচের কথা। ইন্দ্ৰজাল-এর আসল ব্যাপারটুকু লক্ষ করতে হবে। স্যার ফ্রেজার দেখাচ্ছেন :
বিশুদ্ধ ও অবিমিশ্র রূপে যেখানেই…ইন্দ্ৰজাল দেখা দিয়েছে, সেখানেই ধরে নেওয়া হয়েছে যে, প্ৰকৃতিতে কোনো রকম আধ্যাত্মিক বা ব্যক্তিগত কিছুর হস্তক্ষেপ নেই, একটি ঘটনা আর এক একটি ঘটনার অনিবাৰ্য ও নিয়ত অনুগামী। অতএব এর মূল ধারণা এবং আধুনিক বিজ্ঞানের মূল ধারণা অভিন্ন। ঐন্দ্রজালিক ভাবধারার মূলে রয়েছে একটি অব্যক্ত, কিন্তু বলিষ্ঠ ও বাস্তব, বিশ্বাস, সে বিশ্বাস হলো প্ৰকৃতির নিয়মানুবতিতায় বিশ্বাস।…তাই ঐন্দ্রজালিক ও বৈজ্ঞানিক ধারণায় ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য! উভয় ক্ষেত্রেই ঘটনাপরম্পরা নিখুঁত ও সুনিশ্চিত ভাবে নিয়ম মানে, সেই নিযমের ক্রিয়া নিখুঁতভাবে হিসেব করা যায়, আগে থাকতে ঠাহর করা যায়। প্রকৃতি থেকে খামখেয়াল, দৈবাৎ আর অকারণকে বর্জন করা… … …। ধর্ম যেহেতু মেনে নেয় যে, এই পৃথিবী চেতন শক্তির দাস–যে-শক্তিকে তোয়াজ করলে তার উদ্দেশ্য বদলে যেতে পারে,–সেইহেতু বিজ্ঞান এবং ইন্দ্ৰজাল উভয়ই ধর্মের একেবারে বিরুদ্ধ। কেননা উভয় ক্ষেত্রেই ধরে নেওয়া হয়েছে যে, প্ৰকৃতির পথ কোনো ব্যক্তিগত মন-মেজাজের খেয়ালখুশির উপর নির্ভর করে না, তার বদল নির্ভর করে যন্ত্রের মতো চালিত অলঙ্ঘনীয় নিয়মের উপর। ইন্দ্ৰজালের বেলায় এই স্বীকৃতিটা অব্যক্ত, বিজ্ঞানের বেলায় ব্যক্ত।
উভয় উদ্ধৃতিকে দীর্ঘতর করবার প্রলোভন সংবরণ করতে হয়; তবু এটুকু থেকেই আদিম মানুষের নাচে-ইন্দ্ৰজালে মেশা প্ৰাগ্বিভক্ত সংস্কৃতি সম্বন্ধে কয়েকটা মূলসূত্র আবিষ্কার করা যাবে।
প্রথম এ-সংস্কৃতি একের নয়, দশের; ব্যষ্টির নয়, গোষ্ঠীর। বিদগ্ধ ব্যক্তি বা বিদগ্ধ সমাজ বলে আলাদা কিছু নেই, সংস্কৃতি যতটুকু তাতে সকলেই সমান অংশীদার। দ্বিতীয়ত, এ-সংস্কৃতির প্রধান উদ্দেশ্য প্রয়োগ, কর্ম, প্ৰকৃতিকে জয় করা। বিশুদ্ধ জ্ঞান চর্চা বা অবসর বিনোদনের তাগিদ নয়, তাগিদ যেটুকু, সেটুকু কাজের তাগিদ। প্রয়োগের খাতিরেই জ্ঞান, আবার জ্ঞানের দরুন প্রয়োগের উন্নতি-জ্ঞান আর কর্ম পৃথক হয়ে পড়েনি, জ্ঞান আর কর্মের প্রাগ বিভক্ত সমন্বয়। তৃতীয়ত, চেতনকারণবাদের দিকে, ধর্মের দিকে, ভাববাদের দিকে ঝোক নেই। ঝোকটা বহিঃপ্রকৃতিকে বশ করবার দিকে, বহিঃপ্রকৃতির অমোঘ নিয়মকে আবিষ্কার করবার দিকে, এক কথায় বস্তুবাদের দিকেই। তাই বলে সচেতন জড়বাদের উপর ইন্দ্ৰজালের প্রতিষ্ঠা সত্যিই নয়; তা হবার কথাও নয়। আদিম অসভ্য মানুষ দল বেঁধে প্রকৃতিকে জয় করবার চেষ্টা করত, কিন্তু তখন তার সামর্থ্য অতি ক্ষীণ, তার সার্থকতা নেহাতই সংকীর্ণ। বৃষ্টির নাচ নাচলে সত্যিই এমন কিছু বৃষ্টি পড়ার বাস্তব সম্ভাবনা নেই, শিকারের নাচ নাচলেই এমন কিছু মৃগয়া সমাধা হবার কথা নয়। বাস্তব সাফল্যের সংকীর্ণতাকে কাল্পনিক সাফল্য দিয়ে পুরণ করা। ইন্দ্ৰজালের তাই অনেকখানিই ইচ্ছাপুরণ। তবুও তখন এই ইচ্ছাপূরণটুকুও জীবনসংগ্রামের অঙ্গ। এ ইচ্ছাপুরাণ বাস্তব সংগ্রামে উদ্দীপনা জুগিয়েছে। অনেক মানুষ দল বেঁধে একসঙ্গে নাচছে। বৃষ্টির নাচ, কিংবা ভালুক শিকারের নাচ। নাচছে আর ভাবছে, বৃষ্টিকে জয় করা গিয়েছে, জয় করা গিয়েছে শিকার। বৃষ্টি এবার পড়বেই পড়বে, শিকার এবার জুটবেই জুটবে। তারপর দল বেঁধে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়া-মনের সামনে দুলছে কামনা সফল হবার ছবি, আর সেই ছবির কাছ থেকে পাওয়া প্রেরণার ফসল জোগাড় করা, শিকার সমাধা করা অনেক বেশি সহজ! এই প্রেরণাটুকু বাদ দিলে তখনকার ওই ভোঁতা হাতিয়ার হাতে পৃথিবীর সঙ্গে সংগ্রাম অনেক দুরূহ হয়ে দাঁড়াত। তাই ইন্দ্ৰজাল তখন প্ৰকৃতিকে জয় করবার পথে মানুষকে এগিয়ে নিয়ে গেছে অনেক বেশি করে, অনেক ভালো করে।
তারপর প্রকৃতির সঙ্গে দিনের পর দিন একটানা সংগ্রামের চেষ্টায় উন্নত হলো মানুষের হাতিয়ার, আর তাই উৎপাদনশক্তি। মানুষ উৎপাদনা করতে শিখল নিছক বেঁচে থাকবার জন্যে যেটুকু জিনিস দরকার, তার চেয়ে অনেক বেশি জিনিস প্রকৃতির কাছ থেকে সংগ্ৰহ করতে, আর তখন থেকেই সম্ভব হলো অনেকের শ্রমের উপর নির্ভর করে কয়েক জনের পক্ষে শ্রমজীবনে অংশ গ্ৰহণ না করেও বেঁচে থাকা। ফলে, সেই আদিম সাম্যাবস্থা-বিচ্যুতি। শ্ৰেণীহীন সমাজ ভেঙে দেখা দিল নতুন সমাজ; সে সমাজে শ্রেণীবিভাগ, অতএব শ্রেণীসংগ্রামও। আর দেখা দিল ভাববাদ। ইন্দ্ৰজালের বদলে ধর্ম, আর ধর্মেরই সংস্কৃত সংস্করণ ভাববাদ। প্রয়োগের পরিবর্তে নিছক তত্ত্বজিজ্ঞাসার উৎসাহ। অব্যক্ত বস্তুবাদ বা জড়বাদের দিকে ঝোঁক ছেড়ে চেতনকারণবাদের বা ভাববাদের দিকে ঝোঁক।
শ্রেণীবিভাগের পাশাপাশি ভাববাদের উদয়। একে নিছক ঐতিহাসিক আপতন বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। শ্রেণীবিভক্ত সমাজকে বদল করার মধ্যেও ভাববাদের চরম অসম্ভবের হাত থেকে প্ৰকৃত মুক্তি। একে রাজনৈতিক দল-বিশেষের প্রচারমাত্র বলে ব্যঙ্গ করাও অসম্ভব।
আদিম শ্রেণীহীন সমাজ ভেঙে দেখা দিল নতুন সমাজ-শ্রেণীবিভক্ত সমাজ।। একদিকে ব্ৰাহ্মণ-ক্ষত্ৰিয়, অপর দিকে শূদ্র; একদিকে ইসাক-ফেয়ারোপুরোহিত, অপর দিকে বঞ্চিত লাঞ্ছিত ক্রীতদাস; একদিকে শোষক-শাসকের দল, অপরদিকে শোষিত শ্রমিকের দল। দল বেঁধে সবাই মিলে প্ৰকৃতিকে জয় করবার চেষ্টা নয়-প্ৰকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের ভার পড়ল শুধু একদল লোকের উপর; তারাই গতার খাটাবে, মাটি চাষবে, প্রাসাদ গড়বে, মন্দির গাথবে। শ্রমের ভার, কিন্তু শ্ৰমের ফলভোগের অধিকার নয়। সে-অধিকার অন্য শ্রেণীর, শাসক শ্রেণীর। পরান্নজীবী এই যে নতুন শ্রেণীর মানুষ, এদের পক্ষে গতির খাটাবার তাগিদ নেই একটুও; তাই গতর খাটানোটা নেহাতই ইতরের লক্ষণ–“শূকর-যোনি, শ্বা-যোনি চণ্ডাল-যোনি বা” (ছন্দোগ্য উপনিষদ)। চণ্ডাল হলো শুয়োর আর কুকুরের সমগোত্র। গতির খাটাবার তাগিদ এতটুকুও নেই বলেই মাথা খাটাবার দেদার অবসর। চিন্তা বা বুদ্ধি বা জ্ঞানবা যে কোনো নাম দিয়েই এই মাথা খাটানো ব্যাপারটাকে ব্যক্ত করা যাক না কেন-চরম উৎকর্ষ বলে ঘোষিত হলো। এই জ্ঞান-এর উপর শাসক শ্রেণীর একেবারে একচেটিয়া অধিকার, কেননা শোষিত জনগণের উপর গতির খাটাবার ভার, এবং তখন হাতিয়ারের এমন উন্নতি হয়নি যে, জনগণ অল্পমাত্ৰ গতির খাটিয়ে মানবসমাজের মোট অভাব দূর করে বাকি সময়টুকু সংস্কৃতির চর্চা করবে। তাই যাদের উপর গতির খাটানোর দায়, মাথা খাটাবার মতো অবসর তাদের কাছে কল্পনার অতীত। প্ৰাচীন মিশরী প্যাপিরসে লেখা থেকে এখানে কিছুটা উদ্ধৃত করবার প্রলোভন হয়। তখন গতির খাটাবার দায়টা যে আজকের শ্রমিকের দায়ের চেয়ে কিছুমাত্র কম নয়, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে :
কামারকে দেখেছি কামারশালে কাজ করতে। আগুনের মুখে হাপর নিয়ে সে দিনরাত বসে রয়েছে; ওইরকমভাবে একটানা বসে থাকতে থাকতে তার গায়ে পচা আর আঁশটে গন্ধ হয়ে গিয়েছে, … …। খোদাইকর সমস্ত দিন একটানাভাবে কঠিন পাথর কেটে চলেছে, তারপর দিনের শেষে হাত দুটো যখন তার নেহাতই চলতে আর চায় না, তখন হয়তো সারা দিনের মজুরি বাবদ দুমুঠে খাবার জুটল; কিন্তু পরের দিন সুৰ্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যদি সে আবার কাজে না লাগে, তাহলে তার পিঠের দিকে হাত দুটো শক্ত করে বেঁধে … …। রাজমিস্ত্রির কথা বলব? পরনের কাপড় বলতে তার কোমরে শুধু একটা নেংটি, কাজ করতে করতে তার আঙুলগুলো ক্ষয়ে গিয়েছে, কিন্তু তার যদি খিদে অসহ্য হয়, তাহলে নিজের হাত কামড়ানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই।… …হাঁটু দুটো বুকে দুমড়ে চেপে তাঁতি সমস্ত দিন ধরে তাঁত বুনছে, তাই সমস্ত দিন সে ঘরের মধ্যে বন্দি,–“সুর্যের আলো দেখবার জন্যে প্ৰাণটা যদি কখনও একান্ত ব্যাকুল হয়, তাহলে দোরের পাহারাদারকে নিজের রুটিটুকু ঘুষ না দিয়ে উপায় নেই। … … -মুচি যেন সারাটা দিন ধরে কাতরাচ্ছে, তার শরীর পচে গিয়ে পচা মাছের গন্ধ, আর যখন তার পেটের জ্বালা একেবারে অসহ্য হয়ে: ওঠে, তখন তার পক্ষে চামড়ায় দাত ফোটানো ছাড়া আর কোনো গতি নেই……
নীল নদের ধারে মানুষের যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, এই তার অন্দর মহলের আসল চেহারা। কিন্তু শুধু মিশরই বা কেন? এর পাশাপাশি তুলনা করে দেখুন, আমাদের দেশে শ্রেণীসমাজে শূদ্র সম্বন্ধে মনোভাব “মানব” ধর্মে কীভাবে প্ৰকাশ পেয়েছে; তুলনা করলেই বোঝা যাবে, বিভিন্ন প্রাচীন সভ্যতার খোলসগুলোয় যতই তফাত থাক না কেন, সে-সব খোলস ছাড়ালে সবগুলিরই চেহারা মোটামুটি এক :
উচ্ছিষ্টমন্নং দাতব্যং জীর্ণানি বসনানি চ।
পুলকাশ্চৈব ধান্যানাং জীর্ণাশ্চৈব পরিচ্ছদা:।
–শূদ্রের জন্যে ছেঁড়া মাদুর, জীর্ণ বসন, উচ্ছিষ্ট অন্ন।
নোঙর ছবি সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনো আধুনিক রাজনীতিকের কল্পিত প্রচার-পত্র নয়।
এ-হেন যে জনগণ, এদের পক্ষে মাথা খাটিয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞান চর্চার কথা নিশ্চয়ই ওঠে না। ভগবান কী রকমের সুতো দিয়ে স্বৰ্গ থেকে পৃথিবীকে বুলিয়ে রেখেছেন? তিনি কেন সৃষ্টি করলেন মানুষকে, আর মানুষের মধ্যে সেরা মানুষ ফেয়ারোকে? পশ্চিমের কোন পাহাড়ের পিছন দিকে মৃত আত্মার জমায়েত? –এ সব প্রশ্ন জনগণের মাথায় ওঠে নি। মানুষকে এই জনগণ অমৃতের পুত্র বলে কল্পনা করবে। কেমন করে? কখন এরা বসে ভাববো : ওঁ উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ। ‘সোহং ব্ৰহ্ম’ বা ‘তত্ত্বমসি শ্বেতকেতু’, কিংবা ওই ধরনের কোনো মহাবাক্যও এদের কারুর ঠোঁটে ফুটে ওঠবার কথা নয়। শ্রেণীবিভক্ত সমাজ। প্ৰকৃতির সঙ্গে সমবেত সংগ্ৰাম নয়। আর। আসলে সংগ্রাম বেটুকু, সেটুকুর দায় লুষ্ঠিত শোষিত জনগণের উপর; জীবন তাদের কাছে বোঝামাত্র, চিন্তার জাল বোনা দূরে থাকুক, মরবার ফুরন্থতটুকুও তাদের যেন নেই। গতির খাটিয়ে শরীর ক্ষয় করার পথই যেন তাদের সামনে একমাত্র পথ।
আর অপরদিকে মুষ্টিমেয় শোষকের দল। প্ৰকৃতির সঙ্গে লড়াই করবার হাতিয়ার তখন যতই অনুন্নত আর স্থূল হোক না কেন, শোষণের পদ্ধতি এত নির্লজ আর অকুণ্ঠ যে, শোষকের ঘরে বিলাসের প্রাচুর্য। তাই তাদের কাছে প্রয়োগের তাগিদ, প্ৰকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের তাগিদ এতটুকুও নেই; নিছক চিন্তার জাল বোনাই সহজ আদর্শ। যারা খেতি চষে, কাপড় বোনে, পাথর কাটে, প্ৰাসাদ গড়ে, তারা নেহাতই ছোটোলোকের দল; গতির খাটানোটা ইতরের লক্ষণ, মাথা খাটানোর মধ্যেই মানবাত্মার চরম উৎকর্ষ।
মিসমার হয়ে গেল মেহনতের মর্যাদা। কেননা, সভ্যতার যেটা সদর মহল, যেখানে মালিকদলের জমকালো দরবার, সেখানে আর মেহনতকারী মানুষের ঠাই রইল না। মালিকদের পক্ষে দায় নেই মেহনত করবার, গতর খাটাবার। মাথা খাটিয়েই তারা ঠিক করে দেবে, কোনখানে কারা কেমনভাবে মেহনত করবে,-ফসল ফলাবে, কাপড় বুনবে, কাটবে। পাথর, গড়বে ইমারত। কিন্তু যে ক্রীতদাসের দল এই মেহনত করবে, তারা রইল চোখের আড়ালেই, পাইক-পেয়াদার চাবুক দিয়ে ঘেরা ছোট গণ্ডিটুকুর মধ্যে। তাই শ্রেণীবিভাগ দেখা দেবার পর থেকে যে-মন দিয়ে, যে-বুদ্ধি দিয়ে মেহনতের পরিকল্পনা, সেই মনের সঙ্গে, সেই বুদ্ধির সঙ্গে মেহনতকারী হাতের সম্পর্ক গেল ঘুচে। রাজদরবারে বসে মিশরের রাজা আর সভাসদেরা মিলে হয়তো পরিকল্পনা করল, মরুভূমির বুকে পাথর দিয়ে গাথা হােক বিশাল, বিরাট, পিরামিড। কিন্তু শুধু মাথা ঘামিয়ে এই পরিকল্পনাটুকু করেই তো সত্যিকারের পিরামিড গড়া হয় না। তার জন্যে আসলে দরকার লক্ষ মানুষের রক্ত-জাল-করা মেহনত, দীর্ঘ মেহনত। কিন্তু এই মেহনতটা সমাজের সদর মহলের আড়ালে, তাই চোখে পড়ে না। এই মেহনতের দায় ক্রীতদাসের উপর, শূদ্রদের উপর, ছোটলোকদের উপর। তাই এর মৰ্যাদা নেই। দিনের পর দিন মানুষ সভ্যতার কত আশ্চৰ্য চিহ্নই না গড়ে তুলতে লাগল। কিন্তু সভ্যতার এত আশ্চর্য কীর্তির মূলে আসল অবদান যে মেহনন্তের, সেই কথাটা আর মনে রইল না। মানুষ মনে করল, এত সব কীর্তির আসল যে-গৌরব, তা হলো মানুষের মনের, বুদ্ধির, চেতনার। অথচ, চেতনা বা মন বা বুদ্ধি – সব কিছুই যে শেষ পৰ্যন্ত মানুষের মেহনতের কাছে ঋণী, এই কথাটুকু ভুলে গেল মানুষ।
মাথা খাটানো আর গতির খাটানো, পৃথিবীকে চেনা আর পৃথিবীকে বদল করা, কর্ম আর জ্ঞান – শ্রেণীবিভাগ দেখা দেবার পর থেকে যেন চিড় খেয়ে দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। যতদিন দল বেঁধে সমানে সমান হয়ে বাচ, ততদিন মেহনতের উলটো পিঠেই চেতনা, কর্মের উলটো পিঠেই জ্ঞান, দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক বড় নিবিড়। অবশ্যই একথায় কোনো সন্দেহ নেই যে, তখন পর্যন্ত মানুষের হাতিয়ার অনেক স্থূল, তাই মেহনতটাও নেহাতই অনুন্নত, পৃথিবীকে বদল করবার চেষ্টায় বাস্তব সাফল্য নেহাতই সংকীর্ণ। তাই তার উলটো পিঠে যে-চেতনা, সেই চেতনাও অনেকখানি স্থূল, অনেকখানিই ভ্ৰান্ত কল্পনা দিয়ে ভরা। তবু চেতনায় মেহনতে আত্মীয়তা, যে-আত্মীয়তা ঘুচল শ্রেণীসমাজ দেখা দেবার সময় থেকে।
যাকে আমরা দর্শনশাস্ত্ৰ বলি, কিংবা আরো নিখুঁতভাবে বললে, যাকে বলা উচিত অধিবিদ্যা বা metaphysics, তার জন্ম-ইতিহাসের আসল রহস্যটা বুঝতে গেলে মূলসূত্র অনুসন্ধান করতে হবে এইখান থেকেই, সমাজের এই শ্ৰেণীবিভাগ থেকেই। তার মানে এই নয় যে, সমাজে শ্রেণীবিভাগ দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই জন্ম হয়েছে অধিবিদ্যা বা দর্শনশাস্ত্রের। এইভাবে বুঝতে যাওয়াটা যন্ত্রকে বুঝতে যাওয়ার মতো হবে–অর্থাৎ ভুল হবে। তার মানে, হঠাৎ কোনো এক মুহুর্তে ভূমিকম্প হওয়ার মতো সমাজ-জীবনে শ্রেণীবিভাগ ফুটে ওঠেনি। আর কল টিপলেই যে-রকম জল পড়ে, সেইরকমভাবে শ্রেণীবিভাগ দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু জন্ম হয়নি। অধিবিদ্যার আর ভাববাদের। তবু একথাতেও কোনো সন্দেহ নেই যে, যাকে আমরা দর্শনশাস্ত্র বা অধিবিদ্যা বলতে অভ্যস্ত, তার বীজ এই সামাজিক শ্রেণীবিভাগের মধ্যেই; সে বীজ ফলে-ফুলে শোভিত। হয়ে মহীরূহের রূপ নিতে ঐতিহাসিকভাবে অনেক দিন সময় নিয়েছিল নিশ্চয়ই! তবু, সামাজিক শ্রেণীবিভাগের কথাটা ভুলে গেলে দর্শনশাস্ত্রের আসল রহস্যটুকু বুঝতে পারা যাবে না। কেননা, এই অধিবিদ্যা বা দর্শনশাস্ত্রের আসল কথা হলো, বিশ্বের আসল রহস্যকে জানতে চাওয়া-শুধু জানা, শুধু নির্মল, নির্লিপ্ত জ্ঞান। অন্তত, দর্শনশাস্ত্রের যারা ডাকসাইটে পণ্ডিত, তেঁারা মোটের উপর এই কথাটাই মেনে নিয়েছেন। দুনিয়া নিয়ে মাথা ঘামানো, বিশুদ্ধ বুদ্ধি দিয়ে পরম সত্যের একটা বৰ্ণনা খোজা,-দুনিয়াকে বদল করবার কথা নয়।
মেহনত পড়ল চোখের আড়ালে, মেহনতের দাবিটা আর আসলে বড় দাবি হয়ে রইল না। সমাজের সদর মহলে শেষ পৰ্যন্ত চেতনার দাবিটাই চূড়ান্ত দাবি হয়ে দাঁড়াল। এ-চেতনা কিন্তু বিশুদ্ধ চেতনা, মেহনতের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই,- আর মেহনতের সঙ্গে সম্পর্ক নেই বলেই মাটির পৃথিবীর সঙ্গেও সম্পর্ক নেই! কেননা, একমাত্র কাজের মানুষই মাটির পৃথিবীর মুখোমুখি। মেহনতের সময় যখন যুঝতে হয় পৃথিবীর সঙ্গে, তখন না বুঝে উপায় নেই, এই পৃথিবীটা কী নিৰ্ঘাত এক বাস্তব। লাঙল দিয়ে মাটি চাষবার সময় এ-প্ৰশ্ন আর মাথায় আসে না যে, লাঙলটা বাস্তবিকই সত্যি, না মনের একটা ভুল মাত্র, যেমন মনের ভুল হলো অন্ধকার জায়গায়দাঁড়িতে-দেখা সাপ। মাথায় আসে না, খেতটা বাস্তব জিনিস কি-না, তাই নিয়ে মাথা ঘামাবার কথা। কাস্তে হাতে ফসল ফলাবার সময় এ-কথা না-মেনে উপায় নেই যে, কাস্তে আর ফসল দুই-ই হলো অবধারিত সত্য; কামারশালে হাতুড়ি পেটবার সময় টের পাওয়া যায়, হাতুড়ি আর লোহা দুই-ই কী রকম সত্যি জিনিস। কাজের মানুষ বাস্তব দুনিয়ার মুখোমুখি; তার যে চেতনা, সেই চেতনা এই বাস্তব দুনিয়ার প্রতিবিম্ব ছাড়া আর কিছুই নয়।
কিন্তু সমাজে শ্রেণীবিভাগ দেখা দেবার সময় থেকে মেহনতের দায় আর চেতনার দায়,-গতর খাটাবার দায় আর মাথা খাটাবার দায়- দুয়ের মধ্যে সম্পর্ক ভেঙে গেল। যাদের উপর গতরা খাটাবার দায়, তাদের উপর শুধুই গতির খাটাবারই দায়; বাদের উপর মাথা খাটাবার দায়, তাদের উপর শুধুই মাথা খাটাবারই দায়। শুধু তাই নয়। সামাজিক ভাবে মেহনত থেকে বাদ পড়ল মৰ্যাদা। মেহনতকারীর দল হলো নেহাতই অস্পৃশ্য; ওদের মুখ দেখলে পাপ, ওদের ছায়া মাড়ালে পাপ। তাই যারা মাথা খাটায়, তাদের চোখের আড়ালে পড়তে চাইল। এই পৃথিবীটা, যে পৃথিবীর সঙ্গে অস্পৃশ্য মেহনতকারীদের অমন নাড়ির সম্পর্ক। ওরা মশগুল হয়ে উঠল শুধু চেতনাকে নিয়ে–সে-চেতনা বুঝি বাস্তব দুনিয়ার চেতনা নয়–নিছক চেতনা, স্বাধিকারপ্ৰমত্ত স্বয়ত্ত্ব, সর্বশক্তিমান। ফলে এই বিশুদ্ধ চেতনাটাই হয়ে দাঁড়াল আসল সত্য, চরম সত্য। চেতনার দাবিই হলো চরম দাবি, যে জিনিস চেতনার দাবি চোকাতে পারবে না, সে-জিনিস সত্যি হতে পারে না।
এ-কথা অবশ্যই শাসকরাও বুঝেছিল যে, অন্নের উৎপাদন না হলে শেষ পৰ্যন্ত কিছুই টেকে না; কিন্তু তাই বলে অন্নের এই উৎপাদনকেই ধ্রুব আদর্শ বলে মনে করা নেহাতই স্থূল দৃষ্টির পরিচয়! উপনিষদের ভৃগুবরণ সংবাদ-এ এই মনোবৃত্তিরই স্বাক্ষর। বরুণের ছেলে ভূগু-র ইচ্ছে হলো সবচেয়ে চরম সত্যকে জানিবার, তাই বাবার কাছে গিয়ে ভূণ্ড বললেন : ব্ৰহ্ম কী, সে-বিষয়ে আমাকে উপদেশ দিন। বরুণ বললেন : ব্ৰহ্ম সম্বন্ধে একটা বৰ্ণনা শুনলেই ব্ৰহ্মকে তুমি যে জানতে পারবে, এমন আশা নেই; তুমি তপস্যা করো, তপস্যা করলেই ব্ৰহ্মকে জানতে পারবে। (‘তপস্যা’ -দৈনন্দিন প্রয়োগ থেকে অনেক দূরের কথা, বিশুদ্ধ চেতনায় আশ্রয় নেবার কথাই)। তবে একটা মূলসূত্র পেলে তপস্যা করবার সুবিধে হয়। বরুণ তাই মূলসূত্র হিসেবে ছেলেকে বলে দিলেন—‘যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে’, ইত্যাদি। অর্থাৎ, যার থেকে এই সমস্ত জিনিস জন্মেছে, জন্মাবার পর যার উপর নির্ভর করেছে এবং শেষ পর্যন্ত যার মধ্যেই তা বিলীন হয়ে যাবে, তাই হলো ব্ৰহ্ম। এই মূলসূত্রকে অবলম্বন করে ভৃগু তপস্যায় বসলেন, আর তপস্যা করে এসে বললেন; বাবা বুঝেছি, অন্নই হল ব্ৰহ্ম। কেননা অন্ন থেকেই এই সমস্ত উৎপন্ন, ইত্যাদি। বরুণ বললেন : হলো না। কেননা, এ যে নেহাতই স্থূল দৃষ্টির কথা। ভৃগু আবার তপস্যা করতে গেলেন, আর তারপর ফিরে এসে বলেন : বুঝেছি বাবা, অন্ন নয় প্রাণ। বরুণ বললেন : হলো না, আবার তপস্যা করো। তৃতীয়বারের তপস্যায় ভূণ্ড বললেন : মনই হলো ব্ৰহ্ম। চতুর্থবারের তপস্যায় তার মনে হলো : বিজ্ঞানই ব্ৰহ্ম। কিন্তু বরুণ, বললেন; এখনো হয় নি, আরো তপস্যা করতে হবে। শেষবার চরম তপস্যা করে ভৃগু বুঝতে পারলেন, আসলে অন্ন নয়, প্ৰাণ নয়, মন নয়, বিজ্ঞান নয়, –আনন্দই হল ব্ৰহ্ম। আনন্দ থেকেই সব কিছুর জন্ম, ইত্যাদি। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শাসক-শ্রেণীর ভঙ্গি এই উপাখ্যানের ব্যঞ্জনা হয়ে রয়েছে। শুরুতে অন্ন, অন্ন না হলে সমাজের ভিতই যে গাথা হয় না। কিন্তু তাই বলে অন্নকে চরম সত্য হিসেবে স্বীকার করা নেহাতই ছোটলোকমির পরিচয়! স্থূলদুষ্টর অল্পবুদ্ধি মানুষ অন্নকে স্বীকার করুক, নুয়ে পড়ুক অন্ন উৎপাদনের দায়িত্ব কঁাধে নিয়ে। অবশ্যই, শুধু অন্ন উৎপাদনের দায়িত্বই, শুধু কর্মের দায়িত্বই; তাই বলে কর্মফলে অধিকার তো নয়। যারা উচ্চস্তরের মানুষ, কর্মফলের অধিকার তাদের বলেই কর্মজীবনের দায়িত্ব থেকে তারা মুক্ত। তাই তারা ওই ছোটলোকদের মতো অন্ন উৎপাদনের দায় নেবে কেন? তারা এগিয়ে চলুক ধাপে ধাপে অধ্যাত্ম সত্য আবিষ্কারের পথে। ক্রমশ সূক্ষ্ম থেকে সুক্ষ্মতর সত্যের আবিস্কার-শেষ ধাপে আনন্দ, শুধু বিশুদ্ধ চৈতন্যের আনন্দ, আনন্দই ব্ৰহ্ম।
সমাজের এক-প্ৰান্তে একদল নিৰ্বোধ মানুষ। শুধু অন্নের উৎপাদনে নিজেদের শরীর-মন ক্ষয় করে ফেলুক। সমাজের আর-এক-প্ৰান্তে বিশুদ্ধ নিষ্কলুষ চিন্তায় মগ্ন আর একদল মানুষ সূক্ষ্মতম আধ্যাত্মিক সত্য আবিষ্কারই তাদের জীবনে পরম পুরুষাৰ্থ হয়ে থাকুক, আধ্যাত্মিক চেতনার চরমে পৌঁছে তারা হৃদয়ঙ্গম করুক, আনন্দই ব্ৰহ্ম। বিশুদ্ধ আনন্দই হলো বিশ্বরহস্যের চাবিকাঠি।
তাই মার্কস বলেছেন : আধ্যাত্মিক কাজ আর বাস্তব কাজ, এই দুয়ের মধ্যে বিভাগ দেখা দেবার আগে পৰ্যন্ত শ্রমবিভাগ প্ৰকৃত বিভাগে পরিণত হয়নি। সেই সময় থেকে মনে হতে পারে যে, চেতনাটা বাস্তব জগতের চেতনা ছাড়া বুঝি অন্য কিছু। চেতনা যখন থেকে সত্যিই এমন একটা কিছুকে বোঝাতে চায়, যা বাস্তব কিছু নয়, তখন থেকেই আমরা দেখতে পাই সর্ব-সম্পর্ক বিরহিত হয়ে এই চেতনা বিশুদ্ধ মতবাদ, ঈশ্বরতত্ত্ব, দর্শন, নীতিশাস্ত্ৰ প্ৰভৃতি নিয়ে একটা ধর্মমত-জাতীয় কিছুতে পরিণত হয়।
অবশ্য এ কথা ঠিক যে, ইন্দ্ৰজাল ছেড়ে মানুষের তত্ত্বজিজ্ঞাসা একেবারে এক ধাপে বিশুদ্ধ দার্শনিক ভাববাদে পৌঁছোয়নি; ইন্দ্ৰজালের পর ধর্ম, ধর্মেরই বিদগ্ধতম সংস্করণ ভাববাদ। যতদিন শ্রেণীবিভক্ত সমাজ, ততদিনই এই কথা,–ঘুরে ফিরে নানানভাবে নানান পথ দিয়ে যুগে যুগে ভাববাদেই তত্ত্বজিজ্ঞাসার পরিসমাপ্তি। তাই, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উচ্ছেদের মধ্যেই ভাববাদ খণ্ডনের মূলসূত্র। তাই মার্কস বলছেন : এতদিন ধরে দার্শনিকেরা নানানভাবে দুনিয়াকে শুধু ব্যাখ্যা করবারই চেষ্টা করেছেন, কিন্তু আসল কথা হলো একে বদল করা!
০৪. আদিম শ্রেণীহীন সমাজ
আদিম শ্রেণীহীন সমাজ ছেড়ে মানুষ এল শ্রেণীসমাজের আওতায়। কী করে, কোন প্ৰাখিব প্রভাবের ফলে অতীতের মানুষ ইতিহাসের এই পথটুকু অতিক্রম করল? হাতিয়ারের উন্নতি; এই উন্নতিই মানুষকে দেখাল। প্ৰকৃতির কাছে মুক দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবার পথ, আবার এই উন্নতির কৃপাতেই একদল মানুষ ক্ৰমে ক্ৰমে বাকি সকলকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বাধতে পারল। সমাজের এই পরিবর্তন কীভাবে সংস্কৃতির স্তরে প্রতিফলিত হয়েছে, তার কথা মনে রাখতে হবে। আদিম শ্রেণীহীন সমাজ থেকে শ্রেণীসমাজ। আর তারই প্ৰতিচ্ছবি : ইন্দ্ৰজাল থেকে ধর্ম।
ইন্দ্ৰজাল থেকে ধর্ম। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, ধর্ম ইন্দ্ৰজালের উন্নত আর সংস্কৃত সংস্করণমাত্র। বুর্জোয়া পণ্ডিত-মহলে এই ভ্ৰান্ত ধারণা ঘুরে ফিরে অনেকবার দেখা দিয়েছে। অনেকেই চেষ্টা করেছেন ইন্দ্ৰজালের মধ্যেই ধর্মের উৎস খুঁজতে, অনেকে চেয়েছেন ধর্মকে ইন্দ্ৰজালেরই সভ্য সংস্করণ বলে প্রচার করতে। যেন আদিম মানুষের অন্বেষণ-বৃত্তি প্রথমটায় অতি স্থূল আর প্রাকৃত তত্ত্ববোধে আশ্রয় পেয়েছিল, তারই নাম ইন্দ্ৰজাল; ক্ৰমে সেই তত্ত্ববোধ উন্নত আর সংস্কৃত হতে হতে ধর্মের রূপ নিল। অর্থাৎ এই বিচার অনুসারে ইন্দ্ৰজাল আর ধর্ম-র মধ্যে গুণগত তফাত–জাতের তফাত–যেন নেই। তফাত যেটুকু, সেটুকু নেহাতই স্কুলের সঙ্গে সুন্মের তফাত।
অথচ, জাতের তফাতটাই দুয়ের মধ্যে আসল তফাত। ভুয়োদর্শনের সুস্থ প্রভাবের ফলে স্তর জেমস ফ্রেজারের বুর্জোয়া দৃষ্টিও এই বিষয়কে উপেক্ষা করতে পারেনি। তিনিও মানছেন যে, ইন্দ্ৰজালের সঙ্গে ধর্মের শুধু উদ্দেশ্য ভেদই নয়, উপায়-ভেদও বর্তমান। ইন্দ্ৰজালের উদ্দেশ্য হলো প্ৰকৃতিকে বশ করা; প্ৰকৃতিকে জয় কৱা; ধর্মের উদ্দেশ্য হলো দেবতাকে সন্তুষ্ট করে তার কাছে কৃপা ভিক্ষা করা। জয় করা আর ভিক্ষা চাওয়া–উদ্দেশ্যের দিক থেকে গুণগত প্ৰভেদ বই কী। তা ছাড়া, উপায়ের দিক থেকেও তফাতটা অত্যন্ত গভীর ও গুরুতর : প্ৰকৃতিকে বশ করতে গিয়ে ইন্দ্ৰজাল আবিষ্কার করতে চায় প্ৰাকৃতিক নিয়ম-কানুনকে–প্ৰকৃতির রাজ্যে কাৰ্য-কারণ সম্বন্ধকে। তাই, যত অস্পষ্ট আর যত অব্যক্ত ভাবেই হোক না কেন, ইন্দ্ৰজালের পেছনে নিশ্চয়ই এই বিশ্বাসই নিহিত যে, প্ৰকৃতির দাসত্ব থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলো প্ৰকৃতির অমোঘ নিয়মকে চিনতে পারা। ইন্দ্ৰজালের যা প্ৰাপ্য, তার চেয়ে বেশি। উজ্জ্বাস করবার প্রয়োজন নেই-প্রকৃতির দাসত্ব থেকে মুক্তির আসল পথ যে প্ৰকৃতির নিয়মকেই চিনতে শেখা, এই বোধ ইন্দ্ৰজালের পেছনে অব্যক্ত ও অচেতন। কল্পনার কুত্মটিকায় আবিল, তবু এই বোধের অস্তিত্বটুকুকে উড়িয়ে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়। অপর দিকে ধর্মের পেছনে উপায় হিসেবে কোন বোধের উপর নির্ভরতা? প্রার্থনা দিয়ে করুণার উদ্রেক, স্তবস্তুতির খোশামোদ দিয়ে মন গলানো, আহুতির ঘুষ দিয়ে হাত করা। মানুষের প্রথম ধর্ম চেতনা-সব দেশের বেলাতেই মোটামুটি একই রকম-প্ৰকৃতির অধিষ্ঠাতা আর অধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীর সন্ধান করেছে ৷ প্ৰকৃতির রাজ্যে নিয়মের সন্ধান নয়, কেননা এইসব দেবদেবীর মধ্যে আর যাই থাক, নিয়মের শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। খেয়ালী বড়লোকদের মতো এই সব দেবদেবীর দল; অসীম তাদের শক্তি; তবু ভিক্ষে চাইলে তারা ভিক্ষে দিতেও পারে, খোেশামোদ শুনলে খুশি হয়, ঘুষ পেলে সিদ্ধি দেয়।
এবং ফ্রেজার ঠিকই বলেছেন যে, আসলে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের যে বিরোধ, মােটামুটি সেই বিরোধই ইন্দ্ৰজালের সঙ্গে ধর্মের, কেননা अभि रेखांबांनी आधूनिक दिखांप्नब्ररे आनि-भूक्ष। ज्ञ् ऊारेनब्र,-नानांन দেশে নানানভাবে ইন্দ্ৰজাল আর ধর্মের মেশামেশি। সত্ত্বেও,-ফ্রেজার স্পষ্টই অনুভব করেছেন যে, ইন্দ্ৰজাল-কে ধর্মের চেয়ে প্রাচীন বলে স্বীকার করতেই হবে। “যদিও বহু যুগে বহু দেশে দেখতে পাওয়া যায়, ইন্দ্ৰজাল আর ধর্ম মিশে রয়েছে, তবুও কয়েকটি কারণের দরুন মনে করা উচিত যে, এই মেশামিশি আদিম নয়।”
কিন্তু এই সব কারণগুলির স্বরূপ কী? ফ্রেজারের মতে প্ৰধানত দুরকম। প্রথমত, ইন্দ্ৰজাল এবং ধর্মের মূল ধারণাকে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ইন্দ্রজালের ভিত্তি হলো ধারণার অনুষঙ্গ (association of ideas), এবং ধর্মের ভিত্তি হলো প্ৰকৃতির অধিষ্ঠাতা-অধিষ্ঠাত্রী চৈতন্য-এবং-ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন দেবদেবীর কথা। এ কথা তো স্পষ্টই যে, ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন শক্তির ধারণা নিছক ধারণার অনুষঙ্গের চেয়ে অনেক জটিল এবং অনেক উন্নত। দ্বিতীয়ত,–এবং এইটেই হলো ফ্রেজারের বৈজ্ঞানিক মহত্ত্ব যে, পদে পদে তিনি পরিদর্শনের উপর নির্ভর করতে চান–পৃথিবীর বুকে আজও যে সব জাতি সভ্যতার নিম্নতম স্তরে পড়ে আছে, তাদের মধ্যে ধর্ম দেখা দেয়নি, আছে শুধু ইন্দ্ৰজাল। ফ্রেজার বলছেন, অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের কথা। আশ্চৰ্য দেশ এই অষ্ট্রেলিয়া,–এর আকার অপেক্ষাকৃত ছোট, এর মধ্যে জলের অভাব এবং মরুদেশের প্রাচুৰ্য, এবং অন্যান্য মহাদেশের সঙ্গে এর যোগাযোগ না থাকার দরুণ আজও এই দেশ যেন “অতীত জিনিসের জাদুঘর” হয়ে রয়েছে। অন্যান্য দেশে যে-সব গাছগাছড়া আর পশুপাখি আজ লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, সেইসব গাছগাছড়া আর পশুপাখি আজও এখানে টিকে আছে, এবং সেই সঙ্গে টিকে আছে আদিম মানবসমাজের নিদর্শনও। আর সে সমাজে ধর্মের চিহ্ন নেই, আছে ইন্দ্ৰজালের। মোটামুটি বলা যায়, ফ্রেজার বলছেন, অষ্ট্রেলিয়ার সব আদিম অধিবাসীই ইন্দ্ৰজাল-বিদ বা মায়াবী, কিন্তু পুরোহিত একজনও নয়। সভ্যতার এই নিম্নতম নিদর্শনে যদি দেখা যায় শুধু ইন্দ্রজাল, অপেক্ষাকৃত উন্নততর স্তরে ইন্দ্ৰজালের সঙ্গে ধর্মের মেশা মিশি-প্ৰাচীন ভারত, মিশর প্রভৃতি থেকে শুরু করে আধুনিক য়ুরোপের অপেক্ষাকৃত পিছনে-পড়ে-থাকা সমাজ পৰ্যন্ত-এবং সভ্যতার উচ্চতর স্তরে যদি দেখা যায় শুধু ধর্ম, তাহলে বুঝতে হবে সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ইন্দ্ৰজালকে পেছনে ফেলে ক্রমশ এগিয়েছে ধর্মের দিকে।
ফ্রেজারের বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা অসামান্য, এবং এক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধান্তও–ধর্ম এবং ইন্দ্ৰজালে জাতের তফাত, এবং এই দুয়ের মধ্যে ইন্দ্ৰজাল প্ৰাচীনতরঅবশ্যই স্বীকাৰ্য। এবং ইন্দ্ৰজালের প্রাচীনতার পক্ষে উপরোক্ত যে দুটি প্রমাণ তিনি দিয়েছেন, তার মধ্যে দ্বিতীয় প্রমাণের গুরুত্ব নিশ্চয়ই মানতে হবে। কিন্তু তার দুর্বলতা ও দৃষ্টির সংকীর্ণতা ধরা পড়ে উপরোক্ত প্ৰথম প্ৰমাণের মধ্যে। ইন্দ্ৰজাল প্ৰকৃতির অন্তর্নিহিত অমোঘ আইনকানুনকে আবিষ্কার করে প্রকৃতিকে জয় করতে চায়, ইন্দ্ৰজাল আধুনিক বিজ্ঞানেরই আদি পুরুষ-তবুও ইন্দ্রজালের তুলনায় ফ্রেজার ধর্মকে মহত্তর ও উন্নততর মানব-সংস্কৃতি মনে করতে বাধ্য হয়েছেন ৷ এক এই উন্নত লক্ষণ থেকেই প্ৰমাণ, ফ্রেজার মনে করেছেন, যে, ধর্ম উন্নততর মানব-সমাজের সংস্কৃতি। এখানেই ফ্রেজারের বুর্জোয়া দৃষ্টি তাঁর বৈজ্ঞানিক চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছে।
বুর্জেয়া দৃষ্টিকোণের সংকীর্ণতা। সেই সংকীর্ণতা সাম্য-জীবনের স্বরূপএবং তারই প্ৰতিচ্ছবি যে সংস্কৃতিতে, সেই সংস্কৃতির স্বরূপকেও-বোঝাবার পথে পরিপন্থী। তাই, ইন্দ্ৰজাল থেকে ধর্ম, সংস্কৃতির ইতিহাসে এই পথটুকুকে বুঝতে হলে সামাজিক পরিপ্রেক্ষাকে মনে রাখা একান্তভাবে দরকার, মনে রাখা দরকার মানুষের পক্ষে আদিম শ্রেণীহীন সমাজ থেকে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে এসে পড়বার কথা।
আদিম অবিভক্ত সমাজের পটভূমি ছাড়া ইন্দ্ৰজালকে বোঝবার উপায় নেই। কেননা, যত অস্পষ্টভাবেই হোক, যত অচেতনভাবেই হোক, ইন্দ্ৰজালের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানেরই পূর্বাভাস। প্রকৃত বিজ্ঞানের দুটো প্ৰধান দিক ৷ এক হলো প্রয়োগের উপর ঝোক – উৎসাহটা প্ৰকৃতিকে জয় করবার, প্ৰকৃতির সঙ্গে সংগ্ৰাম করবার। আর দ্বিতীয় দিক হলো প্ৰকৃতিকে জয় করবার জন্যে প্ৰকৃতির অমোঘ নিয়মকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা। অর্থাৎ প্ৰকৃত বিজ্ঞানের মূলে এ চেতনা বর্তমান যে, প্ৰকৃতির নিয়মকে চিনতে শেখার মধ্যেই মানুষের প্রকৃত মুক্তি। এই প্রয়োগনির্ভরতা এবং মুক্তির স্বরূপস্বীকারকে বিজ্ঞানের দুটো প্রধান দিক বলে মানতেই হবে, কেননা এর থেকে বিচুত হলে বিজ্ঞানকে লক্ষ্যভ্ৰষ্ট হতে দেখা যায়। যেমনটা হয়েছে আজকের যুগে : সামাজিক অর্থে প্রয়োগভ্ৰষ্ট ও মুক্তি সম্বন্ধে ভ্ৰান্তবিশ্বাস-বিলাসী তথাকথিত বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের যে সংকট গত কয়েক বছর থেকে অত্যন্ত প্ৰকট হয়ে পড়েছে, তাকে ধামাচাপা দেবার উপায়ও আজ যেন নিঃশেষ।
মানুষের সেই আদিম সমাজে, সভ্যতার ওই সুদূর ও নিম্নতর স্তরে, মানুষের সংস্কৃতি কেমন করে এই সুস্থ চেতনার ভিত্তি খুঁজে পেয়েছিল? সমস্যা সন্দেহ নেই। এবং বুর্জোয়ার চুলচেরা বিচারেও এ সমস্যা সমাধানের কোনো মূলসূত্র পাওয়া সম্ভব নয়। কেননা, বুর্জোয়ার দৃষ্টিভঙ্গিই সংকীর্ণ, যে সংকীর্ণতা এই সমস্যা সমাধানের পরিপন্থী। বুর্জোয়ার দৃষ্টি ব্যক্তির ও ব্যষ্টির দৃষ্টি। এই দৃষ্টিতে আদিম সমাজকে বুঝতে পারাই সম্ভব নয়, কেননা সে সমাজ শ্রেণীহীন সমাজ, যেখানে জীবন সমবায়ের জীবন। সে সমাজের অন্তনিহিত স্বজনী উৎসকে বুর্জোয়ার দৃষ্টি আবিষ্কার করবে। কেমন করে? আদিম শ্রেণীহীন সমাজ : একের সঙ্গে দশের সম্পর্ক সংখ্যাগণিতের সম্পর্ক নয়, অঙ্গর সঙ্গে অঙ্গীয় সম্পর্ক। তাই সমগ্র সমাজের কল্যাণ ছাড়া ব্যক্তিবিশেষের মাথায় কল্যাণ সম্বন্ধে আর কোনো কল্পনা আসা কঠিন। মুক্তির রূপ ব্যক্তি-বিশেষের কোনোরকম স্বার্থসিদ্ধি নয়। সমাজের শাসন তখন শ্রেণী-বিশেষের স্বার্থে অনুপ্ৰাণিত হয়নি, তাই মানুষের কাছে সমাজখৃঙ্খলা শৃঙ্খল-এর রূপ নেয়নি ৷ শৃঙ্খলাকে ভেঙে ফেলবার কথা তাই ওঠেই না। বরং এই শৃঙ্খলাকে স্বীকার করা, একে মেনে নেওয়া-তার মধ্যেই মানুষের মুক্তির একমাত্র সম্ভাবনা। একের স্বার্থ আর দশের স্বাৰ্থ পৃথক নয়, দশের সিদ্ধির সঙ্গে একের সিদ্ধির ঘনিষ্ঠ মেশামিশি। সমাজ-শৃঙ্খলা যখন শ্রেণীস্বার্থে রক্ষিত হয়ে শৃঙ্খলের রূপ নেয়, শুধু তখনই মানুষের পক্ষে এই শৃঙ্খলাকে ভাঙবার অন্ধ তাগিদ ওঠে। আদিম প্ৰাগবিভক্ত সমাজে এই তাগিদ ওঠবার কথা নয়। ওঠেওনি। তাই, তার সংস্কৃতির পিছনেও মুক্তি বলতে শৃঙ্খলাকে চিনতে শেখাই বুঝিয়েছে, যদিও অস্পষ্ট, যদিও অচেতনভাবেই।
আদিম প্ৰাগবিভক্ত সমাজের সংস্কৃতিতে প্রয়োগের তাগিদই বা অগ্ৰণী কেন? এর উত্তর জাদুঘরে গিয়ে সে-যুগের ভোঁতা হাতিয়ারগুলোর উপর চোখ বোলালেই বোঝা যায়। ওইরকম স্থূল হাতিয়ার হাতে সবাই মিলে পৃথিবীর সঙ্গে প্ৰাণপণ-সংগ্ৰাম করলে পরই কোনোমতে সবাইকার পক্ষে বাঁচতে পারা সম্ভব। তাই সংগ্রাম যতটুকু, ততটুকু প্ৰকৃতির সঙ্গেই। মানুষের সঙ্গে মানুষের সংগ্ৰাম নয়।
মানুষের উৎপাদন-শক্তি তখনো উদ্ধৃত্ত বলে কিছু সৃষ্টি করতে শেখেনি। বলেই একজনের শ্রমের উপর নির্ভর করে আর একজনের পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়। মেহনতের দায় প্ৰত্যেকের উপরই, মেহনত ছাড়া জীবনের অর্থ নেই। প্ৰকৃতিকে জয় করবার তাগিদটাই আদিম মানুষের কাছে আদি ও অকৃত্রিম তাগিদ; নাচ আর ইন্দ্ৰজালের মধ্যে এই তাগিদের প্রকাশ। শ্ৰীমতী হ্যারিসন দেখাচ্ছেন, আদিম মানুষের সমাজে মানুষের বয়েস বাড়ার আর এক নাম হলো নাচের সংখ্যা বাড়া, নাচে যোগ দিতে না পারাটা চরম লজ্জার লক্ষণ, বার্ধক্যের দরুন নাচে যোগ দিতে না পারলে মানুষ আপন কপালে করাঘাত করে; জীবনধারণের আর কোনো অর্থ খুঁজে পায় না।
প্ৰকৃত বিজ্ঞানের এই মূল ভিত্তিতে–প্ৰয়োগ-প্ৰাধান্য আর মুক্তির স্বরূপবোধে–সুদূর অতীতের অসভ্য মানুষ অচেতনভাবে আশ্রয় পেয়েছিল তার সমাজ-সংগঠনের দরুন। তারপর শ্রেণীবিভক্ত সমাজের ইতিহাসে মানুষ যখন ডাক শুনেছে শোষণের পালা শেষ করে দেবার, তখন আবার বিকশিত হয়েছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের সঙ্গে বস্তুবাদের উপর ঝোঁকও। যেমনটা দেখতে পাওয়া যায় য়ুরোপে, মধ্যযুগ শেষ হয়ে নতুন যুগ শুরু হবার সময়। ইংলেণ্ডে বেকন-হবস, ফরাসী দেশের বস্তুবাদীর দল। কিন্তু ইতিহাসের অগ্রগতির মধ্যে দিয়ে দেখা গেল অতি মারাত্মক ধাঙ্গাবাজি লুকোনো ছিল সে-ডাকের পিছনে; এ-ডাক শোষণের পালা শেষ করবার আহবান নয়, একজাতীয় শোষণের বদলে আর একজাতীয় শোষণকে কায়েম করবার ডাক। আর, এই কথা সমাজের মধ্যে যতই প্রকট হতে লাগল, ততই ক্রমশ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হলো বিজ্ঞানের সংকট। হাজার রকম কলাকৌশলের উন্নতি সত্ত্বেও, লক্ষ রকম চোখ-ধাধানো আবিষ্কারের কান-ফাটানো খবর রটিয়েও, আজ বিজ্ঞানের এই সংকট সম্বন্ধে খবরটুকুকে চাপা দেবার কোনো উপায় পাওয়া যাচ্ছে না। বিজ্ঞানের মধ্যে জায়গা জুড়ে বসতে চাইছে ভাববাদ। নিছক গবেষণারোয় সংকীর্ণ গণ্ডিটুকুর মধ্যে যতটুকু প্ৰয়োগ, তার উপর নির্ভর করেই বেঁচে থাকতে চাইল বিজ্ঞান, সামাজিক মেহনতের বিরাট পটভূমি আর বিজ্ঞানের পটভূমি হয়ে থাকতে পারল না।
সোভিয়েট বিপ্লবের মধ্যে শোনা গেল শোষণের পালা শেষ করবার ডাক। কিন্তু এ ডাক একজাতীয় শোষণ শেষ করে নতুন জাতের শোষণ পেশ করবার অভিসন্ধি নয়। সামাজিক মেহনতের হারানো পটভূমি ফিরে পাওয়া গেল বিজ্ঞানে, ঘোষিত হলো নিঃসংকোচ বস্তুবাদের জয়। তার ভিত্তিতে প্ৰয়োগ, সমষ্টির চেতনা আর মুক্তির স্বরূপ উপলব্ধি। আর তারই প্রেরণায় দিকে দিকে আজ মিলিত মহামানবের অগ্ৰগতি আগামী নিঃশ্ৰেণীক সমাজের দিকে-এই সমাজে বিজ্ঞান হবে সংকটমুক্ত, সমবেত মানবজীবনের উৎস থেকে প্রেরণা সঞ্চয় করে বিজ্ঞান আবার প্রতিষ্ঠিত হবে সুস্থ বস্তুবাদী ভিত্তির উপর।
তবু, আগামী কালের বিজ্ঞান অতীতের ইন্দ্ৰজালের স্তরে নিশ্চয়ই ফিরে যাওয়া নয়। তার সহজ কারণ, আগামী কালের নিঃশ্রেণীক সমাজ অতীতের অবিভক্ত শ্রেণীহীন সমাজের পুনরুক্তিমাত্র নয়। সমবায়ের দিক থেকে, মিলেমিশে একসঙ্গে থাকার দিক থেকে, মিল থাকলেও এ দুইয়ের ঐশ্বর্যে একেবারে আকাশপাতাল তফাত। অতীতের অবিভক্ত সমাজের কাহিনী নিতান্তই দারিদ্র্যের কাহিনী; মানুষ তখন স্থূল হাতিয়ার হাতে প্ৰকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে প্ৰবৃত্ত, তার বাস্তব সাফল্য নেহাতই সংকীর্ণ–তাই দৈন্যের আর অভাবের অন্ত নেই। ওই অক্তাবের প্রতিষেধক হিসেবে মানুষ খুঁজেছে ইচ্ছাপুরাণ-বাস্তব বিজয়ের ফাকিটুকু কল্পনার বিজয় দিয়ে ভরাট করবার চেষ্টা। বজের ডাক-কে আয়ত্ত করে বজের শক্তিকে আয়ত্ত করার কথা। ইন্দ্ৰজালের এইটেই হলো আসল দৈন্য–এই ইচ্ছাপূরণ। দীন সমাজের প্রতিচ্ছবিইন্দ্ৰজালের মধ্যেও অনেকখানি দৈন্য না থেকে উপায় কী? এই দৈন্তের দরুনই, এই ইচ্ছাপূরণের চাপেই, ইন্দ্ৰজালের বস্তুবাদী ভিত্তিটুকু নেহাত অস্পষ্ট এবং অচেতন। আগামী নিঃশ্ৰেণীক সমাজের বাণী হলো প্রাচুর্যের বাণী-তাই দৈন্তের চাপ নেই তার তত্ত্বজিজ্ঞাসায়, আগামী কালের বিজ্ঞানে। সে বিজ্ঞান সুস্থ আর সংস্কারমুক্ত। তার বস্তুবাদী ভিত্তি স্পষ্ট ও সচেতন।
ইন্দ্ৰজাল থেকে ধর্ম। কেমনভাবে, ঠিক কোন প্রভাবের ফলে মানুষের সংস্কৃতির ইতিহাসে এই পরিবর্তন এল? এই পরিবর্তনকে বোঝবার কোনো উপায় নেই। বুর্জোয়ার দৃষ্টি দিয়ে। কেননা বুর্জোয়ার দৃষ্টিকোণ অনিবাৰ্যভাবেই ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টিকোণ, অথচ সংস্কৃতির স্তরে এই পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিচ্ছবিমাত্র; তাই সামাজিক পরিবর্তনটুকুই ঐখানে একমাত্র মূলসূত্র।
সাম্যাবস্থা-বিচ্যুতি। ইন্দ্ৰজালের মৃত্যু এবং ধর্মের জন্ম-এই দুয়ের মূলসূত্রই পাওয়া যাবে এই সাম্যাবস্থা-বিচ্যুতির মধ্যে। একের সঙ্গে দশের সম্বন্ধ আর অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ নয়, একের আর দশের জীবন-সমস্যা নয় অদ্বৈত। একের অনুপ্রেরণা আর দশের অনুপ্রেরণা হলো বিভিন্ন, বিচ্ছিন্ন হলো একের সিদ্ধি আর দশের সিদ্ধি। আদিম সাম্যাবস্থাই ছিল অতীত ইন্দ্ৰজালের মূল উৎস। মানুষের সঙ্গে মানুষের সংগ্ৰাম নয়, মানুষের সঙ্গে সংগ্ৰাম শুধু প্ৰকৃতির। এক অখণ্ড সমগ্রতার মধ্যে মানুষের জীবন, তার সংস্কৃতিটুকুও এই জীবন থেকে বিচ্যুত নয়। তাই সংস্কৃতিটুকুও সংগ্রামেরই অঙ্গ। ইন্দ্ৰজাল তাই প্রয়োগপ্ৰধান। আবার, সমাজ-জীবনে অখণ্ড সমগ্রতা বলেই মুক্তির যে অচেতন আদর্শ ইন্দ্ৰজালের অন্তরালে, তা শৃঙ্খলাকে ভাঙবার আদর্শ নয়,-শৃঙ্খলাকে স্বীকার করার মধ্যেই মুক্তি। তাই সংস্কৃতি হিসেবে ইন্দ্ৰজালের যে-দুটো প্ৰধান বৈশিষ্ট্য, তার মূলে রয়েছে সামাজিক অখণ্ডতার চেতনা। এই আদিম সাম্যাবস্থা-বিচ্যুতির মধ্যেই ইন্দ্ৰজালের মৃত্যুরহস্য।
শুধু ইন্দ্ৰজালের মৃত্যুরহস্যই নয়, ধর্মের জন্মরহস্যও। আদিম সাম্যাবস্থাবিচ্যুতির বিভিন্ন দিকগুলির স্বতন্ত্র উল্লেখ করা যাক, দেখা যাবে প্রত্যেকটি দিকই কীভাবে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধর্মের জন্মকে সম্ভব করেছে। প্রথমত, প্রয়োগের প্রাধান্য আর টিকল না। প্ৰকৃতির সঙ্গে সমবেত মানুষের সংগ্রামের বদলে দেখা দিল মানুষের সঙ্গে মানুষের সংগ্ৰাম। একদল মানুষের ঘাড়ে পড়ল উৎপাদনের সমস্ত দায়। কিন্তু তারা সমাজের সদরমহলে নয়, অন্দরমহলে। তাই সমাজের সদরমহল থেকে বাদ পড়ল মেহনতের কথা। শ্রমের কথা বাদ দিয়ে প্ৰকৃতির ব্যাখ্যা খোঁজবার চেষ্টা। প্ৰকৃতির নানান বিভাগের অধিষ্ঠাতা-অধিষ্ঠাত্রী হিসেবে দেখা দিল হরেক রকম দেবদেবীর কল্পনা। সভ্যতার সদর মহলে মানুষের মন ঝুঁকল ধর্মের দিকে। কিন্তু কোন মানুষের? মানুষ তো আর আগেকার মতো শুধু এক রকমের নয়, দু-রকমের। শাসক আর শাসিত, শোষক আর শোষিত। শুধু শাসকের, শুধু শোষকের মাথা খাটাবার ঢালাও অবসর। মাথা খাটিয়ে পাওয়া দেবদেবীর উপাখ্যান। আর তাই, শাসক-শ্রেণীর চেতনায় জন্ম বলেই, এই সব প্রথম দেব-দেবীগুলি শাসকশ্রেণীর প্রতিকৃতিমাত্ৰ।
প্রথমত, এইসব দেব-দেবীগুলি সকলেই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জীব। এই ব্যক্তিত্ব-চেতনা আদিম সাম্যাবস্থায় ছিল না, থাকবার কথা নয়। কেননা একের চেতনা তখন দশের চেতনার সঙ্গে মিশে এক অখণ্ড সমগ্রতার রূপে বিরাজ করছে। কিন্তু, শ্রেণীবিভাগের পর, শাসকের ব্যক্তিত্ব বাকি সকলোয় উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। তাই এই ব্যক্তিত্ব প্ৰতিফলিত হয়েছে তার কল্পনা দিয়ে গড়া দেব-দেবীগুলির মধ্যেও।
দ্বিতীয়ত, শাসক-শ্রেণীর মানুষের খামখেয়ালী বৃত্তি এই সব দেব-দেবীগুলির মধ্যে অল্পবিস্তর প্রতিফলিত। শাসকের মতোই অসীম শক্তি এই দেবতাদের; তবু তাদের কাছে ভিক্ষে চাইলে ভিক্ষে মিলতে পারে, স্তবস্তুতির খোশামোদে তাদের মন গলাবার সম্ভাবনা, নৈবেদ্যর ঘুষ পেলে তারা সিদ্ধি দিতেও পারে। খোশামোদ-প্রিয় আর লোভী। এই সব প্ৰথম দেব-দেবীর দল-এর মধ্যেই পাওয়া ষাবে পৃথিবীর প্রথম শাসক-শ্রেণীর প্রতিচ্ছবি।
তবু প্ৰকৃতির অধিষ্ঠাতা আর অধিষ্ঠাত্রী হিসাবে কল্পিত হলো কেন? কেননা অপেক্ষাকৃত উন্নত হাতিয়ারের কৃপাতে মানুষের উৎপাদনশক্তি অপেক্ষাকৃত বেশি। হলেও তখনও মূল সমস্যা প্ৰকৃতিকে নিয়েই-প্ৰাকৃতিক শক্তির সামনে মানুষ প্ৰায় তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎ হয়েই রয়েছে। প্রকৃতিকে নিয়ে যে সমস্যা, আদিম সাম্যাবস্থায় মানুষ তার সমাধান করতে চেয়েছিল প্ৰকৃতির সঙ্গে সংগ্ৰাম করে, এই শক্তিগুলিকে জয় করে। কিন্তু সংগ্রামের কথা আর শ্রেণীসমাজে প্রাধান্য পেল না, কেননা তখন কর্ম হয়েছে অপ্রধান, প্ৰাধান্য পেয়েছে জ্ঞান। তাই প্ৰাকৃতিক শক্তি নিয়ে যে সমস্যা, শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের সভ্য মানুষ সে সমস্যার সমাধান করতে চাইল অন্যভাবে। এই শক্তিগুলিকে বাস্তবিক জয় করার চেষ্টা না করে নিজের মনকে, চেতনাকে এমনভাবে বদল করা, যাতে প্ৰাকৃতিক শক্তিগুলি আর শক্রদ্ধাপে দেখা না দেয়। অৰ্থাৎ, নিজের কল্পনাকে আর আবেগকে এমনভাবে পরিবর্তন করে নেওয়া, যাতে অন্তত এইটুকু সাত্মনা জুটবে যে, প্ৰাকৃতিক শক্তিগুলির সঙ্গে মানবমনেরই আত্মীয়তা-এইভাবে বিরোধী শক্তিগুলিকে মিত্র কল্পনা করে মানুষ বুঝি এদের হাত থেকে নিস্তার পাবে। তাই, এই সব আদিম দেব-দেবীর দল-মূলে প্ৰাকৃতিক শক্তি সম্বন্ধে কল্পনা হলেও-শোষক শ্রেণীর চেতনারই ছাচে ঢালা তাদের রূপ। এর মধ্যে প্ৰাকৃতিক শক্তির কাল্পনিক প্ৰতিবিম্ব তো আছেই; কিন্তু শুধু সেইটুকুই নয়, শোষক শ্রেণীর নিজেদের রূপ অনুসারে রূপান্তরিত।
ইন্দ্ৰজাল ছেড়ে ধর্ম। এই ধর্ম শোষকের চিন্তা আর কল্পনা দিয়ে গড়া। তাই এর সঙ্গে শোষক-শ্রেণীর স্বার্থের কথাটাও জড়িত রয়েছে। ধর্মের দরুন শোষক-শ্রেণীর স্বাৰ্থসিদ্ধিটা কী রকম? শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শোষিত জনগণকে শাসনে রাখার জন্যে আধ্যাত্মিক অন্ত্রের উপযোগিতা অসামান্য। স্বৰ্গ-নরক, পাপ-পুণ্য, ইহলোকের অন্নের বদলে পরলোকে পরমামের আশ্বাস, এমনি কতই কী। ধর্ম শিখিয়েছে, সংগ্রামের বদলে প্রার্থনার উপযোগিতা; শাসকের কাছ থেকে যদি কিছু পেতেই হয়, তা নেহাতই ভিক্ষার দান, চাটুকারিতার বখশিশ, ঘুষের ফল। ধর্মকে তাই জনগণকে আয়ত্তে রাখবার আফিম বলে বর্ণনা করা হয়েছে। এ আফিমের ঘোর জনগণের মনকে নেহাতই নিরাপদ, নেহাতই নিরুপদ্রব করে রাখবে।
শ্ৰেণীবিভক্ত সমাজ। ইন্দ্ৰজাল ছেড়ে ধর্ম। শাসক-শ্রেণীর একটি অস্ত্ৰ এই ধর্ম। প্ৰাকৃতিক শক্তির কাল্পনিক প্ৰতিচ্ছবি-শাসক-শ্রেণীর ছাচে ঢালা প্ৰতিচ্ছবি-এই ধর্মের প্রাণবস্তু হলেও বাস্তব হাতিয়ার হিসেবে শাসক-শ্রেণীর কাছে এর মূল্য বড় কম নয়। অবশ্য শ্রেণী-বিভক্ত সমাজের যে রকম ইতিহাস আছে, সেইরকমই ইতিহাস আছে ধর্মেরও। শ্ৰেণীসমাজের কাঠামোর মধ্যে যুগে যুগে উৎপাদনশক্তির রূপ বদলে যাবার ফলে এতদিন পর্যন্ত শোষণের রূপ, সমাজ-ব্যবস্থার রূপ নানানভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। তাই পরিবর্তিত হয়েছে শোষণের জন্যে অনিবাৰ্যভাবে উপযোগী এই আফিমের রূপও।
কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই আফিমকে জনগণ আমনভাবে মেনেই বা নিল কেন? শাসক-শ্রেণীর স্বার্থে প্রণোদিত, শাসক-শ্রেণীর কল্পনাপ্ৰসুত এই ধর্মকে শোষিত জনগণ স্বীকার করতে গেল কেন? ইতিহাসের সেই সুদূর অতীতকে খুঁড়তে পারলে হয়তো দেখা যাবে যে, যতটা সহজে ধর্মকে মেনে নেবার ব্যাপারটা সাধারণত প্রচার করা হয়, আসলে ঘটনাটি অত সহজ সত্যিই ছিল না। অনেক জায়গায় জনগণ অনেকভাবে এই ধর্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলেছিল, বিদ্রোহ ঘোষণা করছিল। তার কিছু কিছু স্বাক্ষর আজও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। তবু, মোটের উপর এ কথায় কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এই ধর্ম-বিশ্বাসকে জনগণ শেষ পৰ্যন্ত স্বীকারই করে নিয়েছে। কেমন করে তা সম্ভব হলো? উত্তরে মনে রাখতে হবে আদিম সাম্যাবস্থাবিচ্যুতির পটভূমি। এই বিচ্যুতির ফলে আদিম সমবেত জীবনে যে নিশ্চয়তা, তারও বিচ্যুতি অবশ্যম্ভাবী। একের ভাগ্য যখন দশের ভাগ্যের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধে যুক্ত, তখন সুনিশ্চিত সাহসে মানুষ বুক বাঁধতে পারে; অনিশ্চয়তার কথা তেমন ওঠে না। কিন্তু মানুষ যখন একা, প্ৰকৃতির বিরাট শক্তির সামনে সে তুচ্ছ আর অকিঞ্চিৎ। এখানে বাস্তব তুচ্ছতা অকিঞ্চন তার কথা বলছি না, তুচ্ছতা-বোধ আর অকিঞ্চনাত-বোধের কথা বলছি। আদিম সাম্যাবস্থায় মানুষের উৎপাদনশক্তি অনেক অনুন্নত ছিল; তাই বাস্তবভাবে দেখতে গেলে প্ৰকৃতির বিরাট শক্তির সামনে মানুষ অনেক বেশি তুচ্ছ, অনেক বেশি অসহায়। তবু, অসহায়বোধ তখন তেমন প্ৰকট হয়ে পড়েনি, যে-রকম প্ৰকট হয়ে পড়ল অপেক্ষাকৃত উন্নত উৎপাদন-প্ৰণালীর সমাজে-শ্রেণী-সমাজে। কেননা, শ্রেণী-সমাজের আগে, এই সাম্যাবস্থায়, একের জীবন যখন দশের জীবনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে যুক্ত, তখন দশের প্রেরণা একের প্রেরণার মধ্যে সঞ্জীবিত। আর সমবায় জীবন থেকে সঞ্জাত এই প্রেরণা বাস্তব অসহায়তা সত্ত্বেও মানুষের মনকে পঙ্গু হতে দেয়নি, মানুষের অসহায়-বোধ প্রকট হতে পারেনি। দশের প্রেরণা একের প্রেরণাকে সঞ্জীবিত করেছে, আর তাই মানুষ দশের সঙ্গে মিলে কোমর বেঁধে লেগেছে অসাধ্য সাধনের কাজে, প্ৰকৃতিকে জয় করবার কাজে ৷ প্ৰকৃতির বিরাট শক্তির সামনে ভীত মানুষ হাটু গেড়ে করুণ প্রার্থনার ভঙ্গি গ্ৰহণ করেনি-মিনতি জানাতে চায়নি। সেই শক্তির কাছে, চায়নি তার করুণার উদ্রেক করতে। দল বেঁধে এক সঙ্গে এই শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করছে মানুষ, এমন-কী বাস্তব বিজয়ের প্রকাণ্ড অসম্পূর্ণতাটা কাল্পনিক বিজয় দিয়ে পূরণ করে নিতে চেয়েছে। কিন্তু কেঁদে পড়েনি, ভিক্ষে চায়নি। কেঁদে পড়া, ভিক্ষা চাওয়া, অসহায়ের মতো করুণা প্রার্থনা করা-সমবেত জীবনের পরিপূর্ণতার মধ্যে এসবের স্থান নেই।
শ্ৰেণী-সমাজের আওতায় জনগণের মধ্যে এই যে অসহায়-বোধ, একে যেন ইন্ধন জোগাল নতুন এক ধরনের দুৰ্যোগ, নতুন এক ধরনের অনিশ্চয়তা। আগে ছিল শুধু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ, শ্রেণী-সমাজে তার উপর জুটল সামাজিক দুৰ্যোগও। বৃষ্টি না হলে ফসল ফলবে না, মানুষের পেট ভরবে না; দল বেঁধে বৃষ্টির নাচ নেচে, কল্পনায় বৃষ্টি পেয়ে দল বেঁধে দ্বিগুণ উৎসাহে ফসলের সন্ধান করা-এই হচ্ছে ইন্দ্ৰজাল। কিন্তু বৃষ্টি পড়ল, ফসল ফলল, তবু মানুষের পেট ভরল না-এ হলো এক নতুন ধরনের অনিশ্চয়তা। অনাবৃষ্টির অনিশ্চয়তার উপর আর এক রকমের অনিশ্চয়তা যোগ করে দেওয়া। মানুষের মনের অসহায়বোধকে দ্বিগুণ করে তোলা। সমবেত জীবন থেকে কোনো প্রেরণারই সঞ্চয় নেই। ভিক্ষাপাত্রই বুঝি একমাত্র সম্বল, শাসকের কৃপা জাগাতে পারা ছাড়া কোনো পথই চোখে পড়ে না। মানুষের মন ধর্মের দিকে ঝুঁকবে বই-কী।
তারপর, সেই প্ৰথম সভ্য সমাজের পর থেকে আজ পর্যন্ত শ্রেণী:সমাজ। উৎপাদন-প্ৰণালীর হাজার উন্নতি সত্ত্বেও এই সামাজিক অনিশ্চয়তার হাত থেকে মানুষ মুক্তি পায়নি। তাই ধর্মের হাত থেকেও নয়। অসহায় মানুষ জীবনে বিধ্বস্ত হয়ে করুণা ভিক্ষা করেছে উচ্চতর শক্তির কাছে। সমবেত জীবন ফিরে না। আসা পৰ্যন্ত এই অসহায়তা থেকে মানুষের মুক্তি নেই। তাই, ধর্মের হাত থেকেও নয়। সমাজের গভীরে ধর্মের এই বীজ লুপ্ত থাকার দরুন। এতদিনকার খাপছাড়া সব রকম নাস্তিক্যবাদ বিফলে গিয়েছে। সমবেত জীবন ফিরে পাবার আগে পৰ্যন্ত ধর্মের হাত থেকে মানুষের প্রকৃত মুক্তি নেই; অর্থাৎ এক কথায় গণ-বিপ্লব। এই বিপ্লব সোভিয়েট দেশে সাম্য-জীবনের আগমনী শুনিয়েছে। তাই, ধর্মের হাত থেকেও নিষ্কৃতির পথ দেখিয়েছে মানুষকে। তবু অতীত ইন্দ্ৰজালের স্তরে ফিরে যাওয়া নয়। অনেক অনেক উন্নত উৎপাদন-প্ৰণালী এসেছে মানুষের কবলে। তাই প্ৰকৃতিকে আসল জয় করবার অভাবটা কল্পনায় জয় করা দিয়ে পূরণ করে নেবার চেষ্টা নয়-ইন্দ্ৰজাল নয়। বিজ্ঞান। সংস্কারমুক্ত সুস্থ বিজ্ঞান। ইন্দ্ৰজালের মূল ভঙ্গি যেন অনেক অনেক উঁচু স্তরে উন্নীত।
ইন্দ্ৰজাল থেকে ধর্ম। শ্রেণীহীন সমাজ থেকে শ্রেণীসমাজ। এই পটভূমিকে মনে রাখতেই হবে। বুর্জোয়া বৈজ্ঞানিক-কলাকৌশলের দিক থেকে যত আশ্চৰ্য প্ৰতিভার অধিকারীই তিনি হোন না কেন-এই পটভূমির কথা মনে রাখেন না। তাই ইন্দ্ৰজাল ছেড়ে ধর্মে পৌঁছোনোর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে শেষ পৰ্যন্ত কয়েকটি কাল্পনিক কথার উপর তাকে নির্ভর করতে হয়।
স্যার জেমস্ ফ্রেজারের কথাই আবার উল্লেখ করছি। ধর্মের জন্মের মূলে মানুষের মনে যে এক অভূতপূর্ব অসহায় ভাব জেগেছিল, সে-কথা তিনি অনুভব করতে পারেন : “আমাদের সেই আদিম দার্শনিকট তার প্ৰাচীন বিশ্বাসের লিঙ্গর থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর, সংশয় এবং অনিশ্চয়তার দুৰ্যোগময় সমুদ্রে ভেসে বেড়াতে বেড়াতে তার নিজের উপর আর নিজের শক্তির উপর পুরোনো সুখের আস্থা নির্মমভাবে ঝাকুনি খাবার পর, নিশ্চয়ই করুণভাবে হতভম্ব ও বিচলিত হয়ে পড়েছিল; শেব পর্যন্ত সে শান্তি পেল ঝোড়ো সমুদ্রে পাড়ি শেষ করে এক শান্ত স্বৰ্গে পৌছে, বিশ্বাস আর কর্মের এক নতুন শৃঙ্খলা খুঁজে পেয়ে, যে শৃঙ্খলা অমন ঝঙ্কাটময় সংশয়ের একটা সমাধান তাকে দিতে পারুল, দিতে পারল প্ৰকৃতির উপর যে আধিপত্যকে সে ইচ্ছের বিরুদ্ধে ত্যাগ করেছে, তারই একটা বিনিময়, বিনিময়টা যতই ঠুনকো হোক না কেন।” কিন্তু প্রশ্ন ওঠে; সহস্ৰ বছর ইন্দ্ৰজাল অভ্যাসের পর হঠাৎ এক সময়ে স্তর ফ্রেজারের ‘আদিম দার্শনিকটর’ মনে এই অসহায় ভাবে জাগল কেন, হঠাৎ বা কেন সে “প্ৰকৃতির উপর আধিপত্য” “ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিত্যাগ” করল? অর্থাৎ, ইন্দ্ৰজাল ছেড়ে মানুষ কেন এল ধর্মের আওতায়? এ প্ৰশ্নকে ফ্রেজার অগ্রাহ করেননি। কিন্তু তার দৃষ্টি বুর্জোয়ার দৃষ্টি, সংস্কৃতির সমস্ত ইতিকথাই সে-দৃষ্টিতে ব্যক্তি-বিশেষের অবদান। তাই তিনি উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলছেন, প্রাচীনকালের “ধূৰ্ততর বুদ্ধিমানেরা” হঠাৎ যেন আবিষ্কার করল ইন্দ্ৰজালের বন্ধ্যাত্বি; বৃষ্টির নাচ নাচলে সত্যিই বৃষ্টি হবার কথা নয়। আর তাই এত অশান্তি, শেষ পৰ্যন্ত ইন্দ্ৰজাল ছেড়ে ধর্মের দিকে অগ্ৰগতি? সংস্কৃতিকে শুধু ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি বলে ধরে নিলে এই রকম অর্থহীন। “হঠাৎ” দিয়ে বিজ্ঞানের অনেক ফাঁক পূরণ করতে হয়!
তবু প্রশ্ন ওঠে, সহস্ৰ বছর ধরে এমন-কী একজনও বেরুল না, যে ধরতে পারল ইন্দ্ৰজালের বন্ধ্যাত্বি? অতি বছর ধরে, অমন একটানাভাবে ইন্দ্ৰজাল টিকল কেমন করে? এ প্রশ্ন ফ্রেজার নিজেই তুলেছেন আর জবাবে বলেছেন : অনেক সময় ইন্দ্ৰজাল অনুষ্ঠানের পর বাস্তবিকই হয়তে হঠাৎ বাঞ্ছিত ফল ফলত। বৃষ্টি তো এমনিতেই মাঝে মাঝে হয়; হঠাৎ হয়তো ইন্দ্ৰজাল অনুষ্ঠানের পর–কিন্তু ইন্দ্ৰজাল অনুষ্ঠানের দরুন নয়, প্ৰাকৃতিক নিয়মেরই দারুন–আকাশ থেকে বৃষ্টি ঝরল। আর তাই মানুষের মনে বদ্ধমূল হলো ইন্দ্ৰজালে বিশ্বাস।
সমাজের পটভূমি তুচ্ছ করে শুধু খাপছাড়া আপতনের উপর নির্ভর করতে যাওয়া। অথচ, স্পষ্টই দেখা যায়, শুধু এই ক্ষীণ আর আপতিক অনুষঙ্গের সূত্র দিয়ে সহস্ৰ বছর ধরে মানুষের পক্ষে ইন্দ্ৰজালে বিশ্বাসের সঙ্গে বাধা থাকবার প্ৰসঙ্গ প্ৰায় হাস্যকর। হাজার বছর ধরে মাত্র কয়েকটি আচমকা ঘটনায় মোহিত হয়ে এবং লক্ষ লক্ষ বিরুদ্ধ দৃষ্টান্তকে অগ্ৰাহ করে মানুষের মনে টিকে রইল ইন্দ্ৰজালে বিশ্বাস! অথচ, সামাজিক পটভূমিটুকু মনে রাখলে এখানে কোনোরকম রহস্য থাকে না। হাজার বছর ধরে মানুষের মন ইন্দ্ৰজালে আস্থাবান ছিল, কেননা হাজার বছর ধরে ইন্দ্ৰজাল সত্যিই প্ৰকৃতিকে জয় করবার পথে তাকে সাহায্য করেছে। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের মানুষ, শ্রেণীসমাজের দৃষ্টিকোণ থেকে ইন্দ্ৰজালের এই বাস্তব অর্থক্রিয়াকারিত্ব বুঝবে কেমন করে? ইন্দ্ৰজালকে আজ শুধু বন্ধ্যা ভ্ৰাস্তির ভূপ বলে মনে হয়, কেননা ইন্দ্ৰজালকে আমরা আমাদের সমাজের পরিপ্রেক্ষায় দেখতে চাই। আজকের দিনে কেউ যদি শিকার-নৃত্য করে, তাহলে তার শিকার সমাধা হবার বাস্তব সম্ভাবনা বাড়বে না। কিন্তু আদিম মানুষের বেলায় তো তা নয়। কেননা, তার জীবন সমবায়ের জীবন-একের সঙ্গে দশের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী। ইন্দ্ৰজালের অনুষ্ঠান কোন মানুষের একার অনুষ্ঠান নয়, সমগ্ৰ সমাজের অনুষ্ঠান। তাই এই অনুষ্ঠান থেকে ষে প্রেরণা উদ্দীপ্ত, তা সমগ্ৰ গোষ্ঠীর মধ্যে সঞ্চারিত। বৃষ্টির নাচ। নাচতে নাচতে সমগ্ৰ গোষ্ঠীর সামনে দুলে উঠল বৃষ্টির ছবি-চোখের সামনে সেই ছবির প্রেরণা। ফসল জুটছে, ফসল জুটবেই, জুটবেই, জুটবেই-এই প্রেরণায় সঞ্জীবিত হয়ে পুরো দল যখন ফসলের সন্ধানে বেরুল, তখন তার বাস্তব সাফল্য অনেক বেশি সম্ভবপর।
তাই যতদিন আদিম অবিভক্ত সমাজ, ততদিন পৰ্যন্ত ইন্দ্ৰজাল বন্ধ্যা নয়, মিথ্যা নয়, মূখীতা নয়। তার বাস্তব মূল্যও অনেকখানি, অনেকখানি তার অবদান বাস্তব সাফল্যের পথে। তারপর সেই আদিম সাম্যাবস্থা-বিচ্যুতিএই বিচ্যুতির মধ্যেই ইন্দ্ৰজালের মৃত্যু : অবিভক্ত সমাজে ইন্দ্ৰজাল যে বাস্তব সাফল্যের সহায় ছিল, বিভক্ত সমাজে আর তা রইল না। মানুষের জীবনে দেখা দিল অনিশ্চিত আর অসহায় ভাব। তাকে অবলম্বন করেই জন্ম হল ধর্মের।
ইন্দ্ৰজাল থেকে ধর্ম : কোনো কল্পিত আদিম দার্শনিকের আকস্মিক আবিষ্কার নয়, সামাজিক পরিবর্তনেরই প্ৰতিচ্ছবি।
০৫. ধৰ্ম আর ভাববাদ
ধৰ্ম আর ভাববাদ। ধর্মেরই মার্জিত আর সংস্কৃত সংস্করণ অধিবিদ্যা, ভাববাদের চুড়ান্ত অসম্ভব থেকে যার মুক্তি নেই। তাই, যে-অর্থে ইন্দ্ৰজাল ছেড়ে ধর্মের আওতায় এসে পড়া, সেই অর্থে ধর্ম ছেড়ে অধিবিদ্যা আর ভাববাদের আওতায় এসে পড়া কোনদিনই নয়। বরং ইতিহাস-বিচারে চোখে পড়ে ধর্মের সঙ্গে অধিবিদ্যার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাই! কেবল, ধর্মের বেলায় দরবারটা আবেগ আর কল্পনার কাছেই বেশি, অধিবিদ্যার বেলায় বিশুদ্ধ বুদ্ধির দাবিদাওয়ার কাছে। তবু মূলের কথাটা একই কথা। সে-কথা মেহনতের কথা নয়, প্ৰকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের কথা নয়, প্ৰকৃতিকে চেনবার,–আর চেনবার ভিত্তিতে জয় করবার,–কথা নয়। প্রয়োগ-জীবন নয়। তার বদলে বিশুদ্ধ চেতনার দাবি। মেহনতের সঙ্গে লেশসম্পর্কহীন চেতনা। তারই বিকাশ ধর্মে, আবার ধর্মেরই বিশুদ্ধ সংস্করণ অধিবিদ্যায়।
আসলে, এই দুনিয়ায় বিপর্যয়ের যেন অন্ত নেই। বিরাট আর বিপুল প্ৰকৃতির যে শক্তি, তারই মুখোমুখি হয়েছে মানুষ। তাই, বিপর্যয়ের পর যেন বিপর্যয়ের ঢেউ। এই বিপৰ্যয়কে জয় করবার পথ রয়েছে দুটো। এক হলো প্ৰকৃতিকে জয় করা, আর এক হলো বিপৰ্যায়-বোধকে জয় করা। এক হলো বিজ্ঞান, যার স্থূল আর অচেতন অভিব্যক্তি ইন্দ্ৰজালের মধ্যে। আর এক হলো ধর্ম, যার সংস্কৃত আর মার্জিত অভিব্যক্তি অধিবিদ্যার মধ্যে।
প্ৰাকৃতিকে জয় করবার পথ, সংগ্রামের পথ–প্ৰয়োগের পথ। অব্যক্ত আর অচেতন ভাবে হলেও, স্থূল আর প্রায় সাহিজিক বৃত্তির বিকাশ হিসেবে হলেও, এই পথটাই ছিল ইন্দ্ৰজালের পথ। আবার এই পথটাই আধুনিক বিজ্ঞানের পথও। বিজ্ঞানের ঐশ্বৰ্য অনেক বেশি, ইন্দ্ৰজালের মতো বিজ্ঞান অচেতন আর অব্যক্ত নয়, নয়। প্ৰায় সাহিজিক বৃত্তির বিকাশমাত্র। ইন্দ্ৰজালের মধ্যে অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে ইচ্ছাপূরণ; কল্পনা আর ভ্রান্তি। তাই আধুনিক বিজ্ঞান ইন্দ্ৰজালের পুনরুক্তিমাত্র নয়। বিজ্ঞানকে খাটো করবার, খেলো করবার, তুচ্ছ করবার তাগিদ ছাড়া আর কোনো তাগিদে নিশ্চয়ই বিজ্ঞানকে ইন্দ্ৰজালের পুনরুক্তি-মাত্র বলবার প্রশ্ন ওঠে না। আসলে ইন্দ্ৰজালের মধ্যে যেটা সংকীর্ণতা,–যেটা ইচ্ছাপূরণ,–তার দায়ভাগ বিজ্ঞানের নয়, ধর্মেরই। তবু ইন্দ্ৰজালের অন্য দিকটার কথা ভুললেও চলবে না। সেটা হলো প্রয়োগজীবনের দিক : কল্পিত দেবতার পায়ে মাথা কোটা নয়, প্রার্থনা দিয়ে মন গলাবার চেষ্টা করা নয়, তার বদলে প্ৰকৃতিকে জয় করা। আদিম মানুষের কাছে মেহনত আর জীবন প্ৰায় সমব্যাপ্ত : এত স্থূল আর এমন ভোঁতা। তার হাতিয়ার যে, সেই হাতিয়ারের নির্ভারে প্রত্যেকের পক্ষেই প্ৰাণপাত মেহনত না করলে বাঁচবার আর কোনো উপায়ই নেই। তাই, চেতনা যেটুকু, তা মেহনতেরই অপর পিঠ। চেতনায়-মোহনতে মিলে এক অখণ্ডতা। মেহনত থেকেই ঠিকরে বেরিয়েছে চেতনার স্ফুলিঙ্গ, আবার চেতনার এই স্ফুলিঙ্গই প্রেরণা জুগিয়েছে মেহনন্তের। তবু হাতিয়ারটা নেহাতই স্থূল, নেহাতই অনুন্নত। তাই তার অনুরূপ মেহনতও নেহাতই নিচু স্তরের। ফলে তার উলটো পিঠেই যে চেতনা, সেই চেতনাও। তার মধ্যে চোদ্দ আনাই ইচ্ছাপূরণ, কল্পনা, ভ্ৰান্তি। তবুও, ভ্ৰাস্তি দিয়ে ভরা হলেও, চোব্দ আনা ইচ্ছাপূরণ হলেও, মেহনতকে প্রেরণা জোগাতে পেরেছে। তার কারণ তখনকার সেই সাম্যজীবন;- যখন সবাই মিলে দল বেঁধে নাচছে, আর সবাইকার চোখের সামনে দুলছে কামনা সফল হবার ছবি, তখন সবকিছুই অনেকখানি অন্য রকম। তখন দল বেঁধে শিকার করতে বেরিয়ে বাস্তবিকই শিকার সংগ্ৰহ করতে পারা অনেক বেশি সহজ, অনেক বেশি সম্ভব। জীবনের তাগিদ, মেহনতের তাগিদ,
প্ৰয়োগের তাগিদ-ইন্দ্ৰজালের মধ্যে এই যে তাগিদ-এরই উত্তরাধিকার আধুনিক বিজ্ঞানের। ইন্দ্ৰজালের ইচ্ছাপূরণটুকুর উত্তরাধিকার নয়; কেননা সেই দৈন্তের ভিত্তি নয়, স্থূল আর প্রায় অকৰ্মণ্য হাতিয়ারের ভিত্তি নয়। প্রয়োগের তাগিদ হলেও, একটা মস্ত তফাত রয়েছে। আদিম মানুষের ইন্দ্ৰজালের পিছনে এই যে প্রয়োগের তাগিদ, এ-তাগিদ প্ৰায় স্বতঃস্ফুর্তভাবে এসেছে তার সমাজের গড়নটা থেকে। সাম্যজীবন, দারিদ্র্যের তাগিদে হলেও সাম্যজীবন। তাই মেহনতের দায় সবাইকার উপরই, মেহনত আর জীবন প্ৰায় সমব্যাপ্ত। অথচ, আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিতে সামাজিক মেহনতের এই প্রেরণা নেই। কেননা আধুনিক সমাজ হলো শ্রেণীবিভক্ত সমাজ, এ-সমাজের সদর মহলে মিসমার হয়ে গিয়েছে মেহনতের মৰ্যাদা। অবশ্য, মধ্যযুগের শৃঙ্খল ভেঙে যখন আধুনিক যুগের শুরু, জনগণ তখন এগিয়ে এসেছে সমাজের সদর মহলে, শোনা গিয়েছে মুক্তির বাণী; সমগ্ৰ মানবতার মুক্তি। সামাজিক মেহনতের প্রেরণায় দীপ্ত হয়ে উঠেছে বিজ্ঞান, ধর্মমোহের সঙ্গে দুর্বার তার সংগ্রাম। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যেই একটা প্ৰকাণ্ড ফাকি লুকোনো ছিল। সমগ্ৰ মানবতার স্বাৰ্থ নিয়ে অত কথার পিছনে প্রচ্ছন্ন ছিল শুধু একটি বিশেষ শ্রেণীর স্বার্থ। সে-শ্রেণীর নাম দেওয়া হয় বুর্জোয়া শ্রেণী। এই শ্রেণীর স্বাৰ্থ যতই প্ৰকট হয়ে পড়তে লাগল, ততই দেখা গেল, সমাজের সদরমহলে জনগণের ঠাই আর হচ্ছে না। বিজ্ঞানের পিছন থেকে বাদ পড়তে লাগল সামাজিক মেহনন্তের প্রেরণা ৷ অথচ, প্রয়োগকে বাদ দিয়ে বিজ্ঞানের পক্ষে বাঁচাই সম্ভব নয়, বিজ্ঞান একান্তভাবেই প্রয়োগনির্ভর। সামাজিক মেহনত থেকে বিচ্যুত হয়ে তাই বিজ্ঞান ক্রমশই নিজেকে গুটিয়ে নিতে লাগল। গবেষণাগারের সংকীর্ণ গণ্ডিটুকুর মধ্যে যে খণ্ড বিচ্ছিন্ন প্রয়োগ, তারই উপর নির্ভর করবার আশায়। এই প্রয়োগটুকুরও নির্ভর যদি না জুটত, তাহলে বিজ্ঞানের পক্ষে বিজ্ঞান হয়ে থাকা আর সম্ভবই হতো না। তবু এপ্রয়োগ নেহাতই খণ্ড প্রয়োগ; সাধারণ কর্মজীবনের সঙ্গে, সামাজিক মেহনতের সঙ্গে তার মুখ-দেখাদেখি কম। কোনো এক অসামান্য বৈজ্ঞানিক হয়তো গবেষণাগারের মধ্যে আবিষ্কার করলেন পরমাণুর ভিতর লুকানোশপ্ৰায় অবিশ্বাস্ত দৈত্যশক্তিকে। কিন্তু সামাজিকভাবে এই দৈত্যশক্তিকে নিয়ে কী করা হবে, তা তার জানা নেই; এই দৈত্যশক্তিকে নিয়োগ করে পাহাড় গুড়ো করে মরুভূমির বুকে নদীর স্রোত টেনে আনা যায়, যায় মরা ধুলোর রাজ্যে সুজলাসুফলা-শস্যশ্যামলা পৃথিবী গড়া। সোভিয়েট দেশে যেমনটা আজ আয়োজন। আবার এই দৈত্যশক্তিকে নিয়োগ করে এক মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ স্ত্রী-পুরুষ আর শিশুকে নির্বিচারে নিঃশেষ করা যায়। মার্কিন মুলুকে যেমনটা আজ আয়োজন। কোন পথে নিযুক্ত হবে ওই দৈত্যশক্তি? নিছক গবেষণাগারের সংকীর্ণ গণ্ডিটুকুর মধ্যে বসে এ-প্রশ্নের কোনো জবাব বৈজ্ঞানিক খুঁজে পান। না। সামাজিক মেহনত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে বিজ্ঞান। বৈজ্ঞানিকের সামনে তাই অনিশ্চয়তার বিরাট খাদ্য। এই খাদ পূরণ করবার আশায় বৈজ্ঞানিককে হরেক রকম অলীক কল্পনার দ্বারস্থ হতে হয়, বস্তুবাদের সঙ্গে মিশেল হয় অধ্যাত্মবাদের। সুস্থ প্রয়োপের যতটুকু ভিত্তি ততটুকুই সুস্থ বস্তুবাদ, কাজের মানুষ অনিবাৰ্যভাবেই বাস্তব পৃথিবীর মুখোমুখি। মধ্য যুগের অন্ধকার বিদীর্ণ করে যখন আধুনিক যুগের দিকে এগিয়ে আসা, তখন সামাজিক মেহনতের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল বলেই বিজ্ঞান রূপ নিতে পেরেছিল দুর্বিজয় বস্তুবাদের। তারপর বিজ্ঞান সামাজিক মেহনত থেকে যতই বিচ্ছিন্ন হয়েছে ততই তার সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত বস্তুবাদী ভিত্তিতে ফাটল দেখা গিয়েছে, দেখা গিয়েছে রকমারি অধ্যাত্মবাদ দিয়ে ফাটলগুলো পূর্ণ করবার চেষ্টা। আবার, কর্মজীবনের সুস্থ তাগিদ ছিল বলেই আদিম ইন্দ্ৰজালের ভিত্তিতেও বাস্তবাদের স্বাক্ষর পাওয়া যায়। প্ৰকৃতির নিয়মকানুনকে চেনবার চেষ্টা। অবশ্যই ভুল করে চেনা। কেননা, তখনকার কর্মজীবন হলো দীন-দরিদ্র হাতিয়ারের কর্মজীবন। প্রয়োগ, কিন্তু নেহাতই নীচু স্তরের প্ৰয়োগ। আর সেই প্রয়োগ-বিছুরিত যে বস্তুবাদ, সে-বস্তুবাদও সুপ্ত, অব্যক্ত, অচেতন। যেন বস্তুবাদের স্বপ্ন, তবুও বস্তুবাদেরই স্বপ্ন-ভাববাদ নয়, অধ্যাত্মবাদ নয়, অলীক ইচ্ছাপূরণের যতখানি মিশেলাই থাকুক না কেন! সোভিয়েট দেশে সেই হারিয়ে-যাওয়া সাম্যজীবনকে নতুন করে খুঁজে পাবার আয়োজন; কিন্তু অভাবের ভিত্তিতে নয়, দারিদ্র্যের ভিত্তিতে নয়, ভোঁতা। আর স্থূল হাতিয়ারের ভিত্তিতে নয়। তাই সামাজিক মেহনতকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করতে পারা, কিন্তু এবার অনেক উচু স্তরে। তুলনাই হয় না, এমন উচু স্তর। আর তাই বলিষ্ঠ, সচেতন বস্তুবাদ। এই বস্তুবাদের আভাস পাওয়া গিয়েছিল আধুনিক যুগের শুরুতে। কিন্তু ওই আভাস হিসেবেই শেষ হলো তার ইতিহাস। সামাজিক মেহনতের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের পিছনে প্ৰকাণ্ড ফাকি ছিলো, তাই। তাই দর্শনের আঙিনায় আসন পাবার জন্য সে-বস্তুবাদ যখন বড় বেশি দুবিনীত হই-হল্লা করেছিল, তখন শ্রেণীসমাজের সদর মহলের সংস্কৃতি নেহাতই অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার জন্যে, খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু সামাজিক মেহনতের সঙ্গে সম্পর্ক যত ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল ততই তাকে সংস্কৃত করবার নামে সর্বস্বাস্ত করে। নেবার আয়োজন, আর না-হয় তো সাক্ষাৎ-সমরে তাকে পরাভূত করে তারই শবদেহের উপর অধ্যাত্মবাদের প্ৰেত-সাধনা। ভারতীয় সংস্কৃতিতে বস্তুবাদের কথা নিয়ে পরে স্বতন্ত্র আলোচনা তুলব। আপাতত ঘুরোপীয় সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখা যাক। আদিম ইন্দ্ৰজালের মধ্যে বস্তুবাদ দেখা দিয়েছিল, যদিও তা স্বপ্নের মতো অক্ষুট। ভিত্তিতে হাতিয়ারের দৈন্য, তাই অক্ষুট, তাই স্বপ্নের মতো। আধুনিক যুগের শুরুতে দেখা দিয়েছিল সুস্থ আর সচেতন বস্তুবাদের আভাস, কিন্তু সমাজ-ব্যবস্থার মূলে যে-ফাকি লুকোনো ছিল তারই চাপে এই বস্তুবাদের ইতিহাস উপক্ৰমণিকাতেই পরিসমাপ্ত হলো। সোভিয়েট সমাজে সামাজিক মেহনতের বলিষ্ঠ ভিত্তি, তাই বিজ্ঞানের ঐশ্বর্ষে দীপ্ত বস্তুবাদ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দুর্জয় হয়ে উঠেছে। বাকি থাকে গ্ৰীক যুগের কথা। দর্শনের ইতিহাসের সঙ্গে সমাজ-ইতিহাসকে মিলিয়ে দেখলেই দেখতে পাওয়া যায়, গ্ৰীক যুগে যখনই বস্তুবাদ দুৰ্জয় হয়ে উঠেছে তখনই তার সঙ্গে কর্মজীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক : প্ৰাচীন আয়োনীয়া শহরে তখন বণিক শ্রেণীর শাসন, পৃথিবীর সঙ্গে সংগ্রামের হাতিয়ারকে উন্নত করার উপরই তাদের সম্পদের নির্ভর, তাই এই উন্নতি-কল্পে তাদের অমন উৎসাহ, আর তাই এই শহরের আবহাওয়ায় জন্ম হলো যে-দর্শনের, সে-দর্শন বস্তুবাদী দর্শন।। থ্যালিস, এ্যানেক্সিমেণ্ডার, এ্যানেক্সিমেনিস। এদের বস্তুবাদ অবশ্যই স্থূল ধরনের বস্তুবাদ। না-হয়ে উপায়ও ছিল না। মানব-ইতিহাসে তখন সবেমাত্র বিজ্ঞানের সুচনা। তাছাড়া ও-শহরে তখন কর্মজীবনের যে-আবহাওয়া, সে-আবহাওয়ার মধ্যে চোদ্দ আনাই ফাকি, কেননা তার ভিত্তিতে শ্রেণী-স্বাৰ্থ আর শোষণই। আর তাই–সমাজের ভিত্তিতে শ্রেণীর স্বার্থের এই উর্বর জমি ছিল বলেই,– আয়োনীয় বস্তুবাদকে অমন সহজে ফেলে গ্ৰীক যুগে পাইথাগোরাস আর পারমানাইডিসের দল পারল ভাববাদী আর অধ্যাত্মবাদী দর্শনের বীজ বুনতে, সে বীজ ফলফুলে শোভিত হয়ে দেখা দিল প্লেটোর দর্শনে। প্লেটো যে কী পরিমাণে এদের কাছে ঋণী, তা নিয়ে গ্ৰীক দর্শনের ঐতিহাসিকেরা অনেক আলোচনা করেছেন। মাঝখানে বস্তুবাদ মাথা তুলে দাঁড়াতে চেয়েছিল এম্পিডোক্লিস্ আর বিশেষ করে ডিমোক্রিটাস-লিউসিপাসের দর্শনে। মনে রাখতে হবে, পাইথাগোরাস, পারমানাইডিস বা প্লেটোর মতো এই বস্তুবাদীরা কেউই কর্মজীবন-বিচ্যুতি রহস্যবাদের বা বিশুদ্ধ চেতনার উপাসক নন। কর্মজীবনের সঙ্গে এদের যোগাযোগটুকু স্পষ্ট, আর তাই বস্তুবাদের বেশ। এম্পিডোক্লিস স্পষ্টই স্বীকার করেন যে, তার দার্শনিক ধারণাগুলিকে তিনি সংগ্রহ করেছেন রঙমেশানো বা রুটি তৈরি করার কাজ চোখে দেখতে দেখতে। তা ছাড়াও গ্ৰীক যুগের অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সঙ্গে তার নাম সংযুক্ত হয়ে রয়েছে, যে-রকম থ্যালিসের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আছে এঞ্জিনিয়ারিং বুৎপত্তির কথা। আর ডিমোক্রিটাস-লিউসিপাস-এর প্রধানতই ছিলেন। বৈজ্ঞানিক, বৈজ্ঞানিক বলেই প্রয়োগপরায়ণ আর তাই বস্তুবাদী। কেবল মনে রাখতে হবে, গ্ৰীক যুগের এইসব বস্তুবাদ মানব-সংস্কৃতির যত মূল্যবান ঐতিহাই হোক না কেন, এগুলি সবই দ্বিধাভিরা বস্তুবাদের নমুনা। কেননা এর মূলে যে প্রয়োগ, যে কৰ্মজীবনের প্রেরণা, তার শক্তি নেহাতই ক্ষীণ। সামাজিক মেহনতের পূর্ণ প্রেরণা এইসব বস্তুবাদের মূলে জোটেনি। জোটবার কথাও নয়। গ্ৰীক সমাজ ক্রীতদাসের মেহনতের উপর নির্ভর করেছিল, সমাজের সদর মহলে মেহনতের পূর্ণ মর্যাদা জুটবে কেমন করে? তবুও, এই সামাজিক কাঠামোর মধ্যেও, মেহনতের সঙ্গে, কর্মজীবনের সঙ্গে যখনই সংস্কৃতির যোগাযোগ, তখনই মাথা তুলে দাড়াতে চেয়েছে বস্তুবাদ। এই কথাটাই বিশেষ করে লক্ষ করবার মতো কথা।
প্ৰাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি মানুষ। বিপৰ্যয়-মুক্তির দুটো পথ তার সামনে। একটা পথ হলো বিপৰ্যয়কে জয় করবার পথ, প্রয়োগের পথ। এই পথে এগুতে গেলে তার চেতনা বস্তুবাদী না হয়ে পারে না। যদিও এ পর্যন্ত–অর্থাৎ সোভিয়েট দেশে সচেতন ঐশ্বর্যের ভিত্তিতে মানুষের মেহনতাকে প্ৰতিষ্ঠা করবার যে-আয়োজন তার আগে পর্যন্ত–প্ৰকৃতিকে জয় করবার যে-পথ, সেপথে নানান দ্বিধা, নানান দ্বন্দ্ব। তাই সোভিয়েট দেশে বস্তুবাদের প্রতিষ্ঠাই প্ৰথম সর্বাঙ্গীণ আর বলিষ্ঠ প্ৰতিষ্ঠা।
আর একটা পথ হলো এই বিপৰ্যায়-বোধকেই জয় করবার পথ। এই দ্বিতীয় পথটারই নাম ধর্ম, যার সংস্কৃত সংস্করণ অধিবিদ্যা আর ভাববাদ। বিপৰ্যয়বোধকে জয় করা। তার মানে, মানুষের যে-চেতনায় এই বিপর্যয়ের প্রতিচ্ছবি, সেই চেতনার উপরেই এমন প্ৰলেপ দেওয়া, এমনভাবে সেই চেতনাকে বদল করে নেওয়া, যাতে বিপৰ্যয় থাকলেও বিপৰ্যয়-সংক্রান্ত হুশিটুকু না থাকে। এই পথই হলো ধর্মের পথ। কেননা, ধর্ম চেয়েছে মানুষের ভাব-আবেগকে এমনভাবে বদল করতে, যাতে প্ৰকৃতি আর বিরুদ্ধ-শক্তি হিসেবে প্ৰতীত না হয়। মানুষের প্ৰথম ধর্ম-চেতনায় তাই দেখতে পাওয়া যায় প্ৰাকৃতিক শক্তির অধিষ্ঠাতাঅধিষ্ঠাত্রী দেবদেবীর কল্পনা : ইন্দ্ৰ, বরুণ, মাতিরিশ্বন, অগ্নি, আদিত্য, সোম, এই রকম সব দেশেই। এই সব প্ৰাচীন দেবদেবীর মধ্যে কিন্তু মানুষের প্ৰতিবিম্ব; তোয়াজ করলে এরা তুষ্ট হয়, তোয়াজ না করলেই সর্বনাশ। তবু সর্বনাশ-সম্ভাবনার বোধ থেকে অন্তত একরকমের মুক্তি তো জুটল; নৈবেদ্য সাজিয়ে উপাসনা করতে পারলে আর সর্বনাশের ভয় নেই। অবশ্যই এ-পথ সত্যিকারের বিপর্যয় থেকে মুক্তি পাবার বাস্তব পথ হতে পারে না। সে পথ একমাত্র বিজ্ঞানের পথ। ধর্মের পথ হলো নিজের মনকে বদল করবার পথ, নিজের চেতনাকে বদল করবার পথ, যাতে সর্বনাশ-বোধ থেকে আত্মরক্ষণ করা যায়। সমাজে শ্রেণী-বিভাগ দেখা দেবার আগে পর্যন্ত এইভাবে চেতনাকে, শুধু চেতনাকে বদল করবার সম্ভাবনা মানুষের সামনে দেখা দেয়নি। দেখা দিল শ্রেণীবিভাগ ফুটে ওঠবার পর থেকে, কেননা তখন থেকেই সমাজের সদর মহলে চেতনা, অন্দরমহলে মেহনত ৷ যে-হাত দিয়ে মেহনত সেই হাত পড়ল চোখের আড়ালে।
অবশ্যই ধর্মের ইতিহাস আছে। বহুর উপাসনা থেকে এক পরমব্রহ্মের ধ্যান পৰ্যন্ত। তবু, এই ইতিহাসের মধ্যে তৈলধারার মতো অবিচ্ছিন্ন যে কথা, সে কথা হলো চেতনাকে বদল করে বিপৰ্যায়-বোধের হাত থেকে নিষ্কৃতি খোঁজবার কথা। প্ৰকৃতিকে বদলে বিপৰ্যায়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি খোঁজবার ঠিক উলটো। প্রয়োগের ঠিক উলটো। বিজ্ঞানের ঠিক উলটো।
ধর্মের মার্জিত আর সংস্কৃত সংস্করণ হলো অধিবিদ্যা, যার মূল কথা চেতনকারণবাদ, ভাববাদ। তাই ধর্মের সঙ্গে অধিবিদ্যার মেশা মিশি। আমাদের দেশে এক চাৰ্যাক-দৰ্শন আর প্রাচীন সাংখ্য দর্শনের কথা বাদ দিলে এ-কথা একেবারে প্রকট ও স্পষ্ট। তাও সাংখ্য দর্শনের নিরীশ্বর প্রধান কারণবাদকে শুধরে নিয়ে তার মধ্যে ঈশ্বরের জন্যে, ধর্মের জন্যে জায়গা করে নেওয়া এবং পাছে বস্তুবাদের মোহো পড়ে চরিত্র বিগড়ে যায়। এই ভয়ে যোগদর্শনের সঙ্গে তাকে একসূত্রে বেঁধে দেওয়া; যে-কারণে শেষ পর্যন্ত সাংখ্য আর শুধু সাংখ্য -রইল না, দেখা দিল সাংখ্য নামের এক দর্শন, যার মধ্যে ধর্মে-অধিবিদ্যায় সুনিশ্চিত মেশামিশি। চাৰ্যাকদের কথা পরে আলাদা করে আলোচনা করব। আপাতত বাকি দার্শনিক মতবাদগুলির দিকে দেখা যাক। এমন কী বৌদ্ধ আর জৈন দৰ্শন-যেগুলির নাম হলো নাস্তিক দৰ্শন-সেগুলির মধ্যেও চোদে আনা প্রেরণা নিছক ধর্মের প্রেরণাই। বৌদ্ধ ধৰ্ম আর জৈন ধর্ম। ধর্মবিরোধী বলে এগুলির নাম নাস্তিক নয়, বেদ মানে না বলে নামটা নাস্তিক। বাকি থাকে আস্তিক দর্শনগুলির কথা। অপৌরুষেয় বৈদিক বিশ্বাসের মুকুট পরে সেগুলি স্পষ্টতমভাবেই ধর্মের সঙ্গে নিজেদের সৌহার্দ ঘোষণা করছে। ন্যায়-বৈশেষিকও মাথা খুঁড়েছে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার আশায়, রামানুজ আর শঙ্কর তর্ক তুলছেন যো-জানের দরুন মুক্তি বা ব্ৰহ্মলাভ সেই জ্ঞান উপাসনাজন্য না বাক্য-জন্য। এইভাবে ধর্ম আর অধিবিদ্যার মেশামিশি সমস্ত ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।
কিন্তু শুধু ভারতীয় দর্শনের কথাই নয়। য়ুরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে নেহাত প্রয়োগপ্রণোদিত বস্তুবাদের গণ্ডিটুকুর বাইরে সর্বত্র এই কথা। পাইথাগোরাস, পারমানাইডিস, প্লেটো থেকে শুরু করে ব্রাডলির ব্রহ্মবিদ্যা পৰ্যন্ত। কেবল, খুব হালে ব্যাপারটার কিছুটা ভোল বদলেছে। সোজাসুজি ভগবানের কথায় সহজে আর মানুষের মন ভোলানো যায় না দেখে ধর্মবিশ্বাসের কথাটা খিড়কি দোর দিয়ে নিয়ে আসবার চেষ্টা : সামনে বহুরূপী, বিজ্ঞানৰ্ম্মান্য প্ৰবঞ্চনার তোরণ। তাই ধর্মের সঙ্গে অধিবিদ্যার বিরোধ নয়, বরং ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়তাই। বিরোধ বস্তুবাদের সঙ্গে বিজ্ঞানের। দর্শনের ইতিহাসে কয়েকটি প্ৰাচীন পরিচ্ছেদের উপর একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। প্রাচীন গ্রীসে যখন কিনা দর্শনের প্রথম জন্ম, তখন তার সঙ্গে প্রয়োগজীবনের কতখানি সম্পর্ক। তাই সে দর্শন কী-রকম অভ্রান্তভাবেই বস্তুবাদী, আর ওই বস্তুবাদের একটা চেষ্টাই হলো ধর্মবিশ্বাসকে, পৌরাণিক বিশ্বাসকে ঠেলে সরিয়ে বিজ্ঞানের প্ৰতিষ্ঠা। কিন্তু ওই প্রয়োগজীবনের সঙ্গে দার্শনিক চেতনার সম্পর্ক যখনই যত ক্ষীণ হয়েছে, ততই সে চেতনা সরে গিয়েছে বস্তুবাদের দিক থেকে ভাববাদের দিকে। এই হলো একটা দেশের কথা।
আরো একটা দেশের কথা তুলব। আমাদের দেশের কথা। আমাদের দেশের প্রাচীন বস্তুবাদী দর্শনটার কথা, যার নাম হলো কিনা চাৰ্য্যাক বা লোকায়ত দর্শন।
প্ৰথমে গ্ৰীক দর্শনের আদি যুগটার কথা; বস্তুবাদ ছেড়ে ভাববাদের দিকে ঝোকার ইতিহাসটা।
০৬. আইয়োনীয় দর্শন
আজকাল দার্শনিক বলতে, অন্তত চলিতভাবে, আমাদের মনে আসে একরকম আধপাগলা ধরনের মানুষের কথা, বিশ্বের চরম রহস্য-চিন্তায় এমনই সে মশগুল যে সাধারণ কর্মজীবনে খুঁটিনাটির ব্যাপারেও তার ঔদাসীন্য–তার চালচলন, এমন কী তার চেহারাতেও নাকি এই ঔদাসীন্যের ছাপ। হয়তো চুল আঁচড়ায় না, দাড়ি কামায় না, জামার বোতাম আঁটতে ভুলে যায়, কিংবা জামাটাই গায়-গলায় উলটো করে; বাজারে চালের দর কত জিজ্ঞেস করলে তার মুখে অসহায় শিশুর ভাব ফুটে ওঠে, পুঁথিপত্র নিয়ে সে যখন তন্ময় তখন ঘরে আগুন লাগল কি-না লাগল এ খেয়ালটুও তার থাকে না। এই বুঝি জাত দার্শনিকের নিখুঁত ছবি; একান্ত জ্ঞানবিভোর, আর তাই যেন একান্ত অকৰ্মণ্য! দার্শনিক বলতে এমনতর ছবি কেন আমাদের মনে উকি দেয়? তার কারণ, আধুনিক দুনিয়ায় জ্ঞানচর্চা আর মেহনত-জীবনের মধ্যে দেখা দিয়েছে বিশাল গভীর খাদ, কিংবা, যা একই কথা, তত্ত্বান্বেষণের সঙ্গে সামাজিক মেহনতের সম্পর্ক গেছে ঘুচে। আর তাই দার্শনিক বলতে আমরা বুঝি নিছক জ্ঞানবিভোর এক মানুষ, সহজ কর্মজীবনের দিক থেকে চেয়ে দেখলে যাকে কিন্তুতকিমাকার দেখায়। কাজের মানুষ তাই ঠাট্টা করে বলে; দর্শন হলো এক অন্ধের পক্ষে এক অন্ধকার ঘরে একটা কালো বেড়ালের সন্ধান, ঘরটায় অবশ্য কোনো বেড়ালেরই চিহ্ন নেই।
অথচ, দর্শনের এ হেন দুর্নাম এমন কিছু চিরকেলে দুর্নাম নয়। ইতিহাসবিচারে দেখতে পাওয়া যায়, কোনো কোনো যুগে সামাজিক মেহনতের সঙ্গে দর্শনের আর দার্শনিকের নিবিড় আত্মীয়তা ফুটে উঠেছে। দার্শনিক বলতে তখন কোন চিন্তাবিলাসীর ছবি মনে আসে না। তখন প্ৰকৃতবিজ্ঞানের যে ইজত। দার্শনিকেরও সেই ইজ্জত, প্ৰকৃত বিজ্ঞানের যে সামাজিক প্ৰতিষ্ঠা দর্শনেরও সেই সামাজিক প্ৰতিষ্ঠা; অর্থাৎ, তত্ত্বান্বেষণ আর কর্মজীবনের মধ্যে যখন যোগাযোগ, তখন দর্শন আর বিজ্ঞানের মধ্যে সীমারোখাটা অস্পষ্ট, কিংবা, যা প্ৰায় একই কথা, দর্শন তখন প্ৰকৃত অর্থে বিজ্ঞানে পরিণত।
যে-যুগে ইওরোপীয় দর্শনের জন্ম সেই যুগ সম্বন্ধে এই কথাই। আর ইওরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে সকলেই র্যাকে আদি দার্শনিক বা প্ৰথম দার্শনিক বলে স্বীকার করেন, তিনি মোটেই নিছক তন্ময় চিন্তাবিলাসী ছিলেন না। বরং তাঁর বৈজ্ঞানিক প্ৰতিভা, কর্মজীবনে কৃতিত্ব বা ব্যবহারিক সাফল্য তখনকার যুগের তুলনায় অসামান্য বলেই স্বীকৃত।
ইওরোপীয় সংস্কৃতির অন্যান্য নানান দিকের মতো ইওরোপীয় দর্শনেরও জন্মভূমি হলো গ্রীস। গ্রীকদের মধ্যে যিনি প্ৰথম দার্শনিক তার নানা থ্যালিস। যীশুখ্ৰীষ্ট জন্মাবার ৬৪০ বছর আগে তাঁর জন্ম এবং নব্বই বছর বয়সে, অর্থাৎ, যীশুখ্ৰীষ্ট জন্মাবার ৫৫০ বছর আগে, তার মৃত্যু।
অবশ্য, শুধু গ্ৰীক বললেই কথাটা স্পষ্ট হয় না। ইওরোপের মানচিত্রটা একবার মনে করুন : গ্রীসের পুর্বদিকে যে সমূদ্র তার ওপারে ছোট ছোট স্বীপ, তারপর তুর্কি। তুর্কির পশ্চিমে অনেকখানি উপকূল অংশকে ছোট এশিয়া বা এশিয়া মাইনর বলা হয়। প্ৰাচীনকালে গ্রীকদের প্রধান চারটি জাতির মধ্যে আয়োনীয় নামের জাতি এই এশিয়া মাইনর-এ এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। সে উপনিবেশের যে-বারোটি শহরের কথা ইতিহাসে প্ৰসিদ্ধ, তারই ভিতর একটি শহরের নাম মিলেটাস, আর যে অঞ্চলে এই মিলেটাস শহর সেই অঞ্চলেরই নাম আয়োনিয়া। ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকে আয়োনীয়দের তখন খুব নাম-ডাক। এমন-কী, তখনকার দিনেই ওরা আমাদের দেশ পর্যন্ত সওদাগরি করতে আসত; খুব সম্ভব ওদের নাম থেকেই আমাদের দেশে “যবন” শব্দ প্ৰথম চালু হয়।
আয়োনীয়দের এমন যে সরগরম ব্যবসা-বাণিজ্য, তার একটি প্ৰধান ঘাটি ছিল ওই মিলেটাস শহর। আর এই কর্মমুখর শহরেই জন্ম হলো ইওরোপীয় দর্শনের, থ্যালিস ছিলেন এই শহরের বাসিন্দা। সওদাগরি শহরটার আবহাওয়া আর তখনকার দিনের যে সমাজব্যবস্থা তার ছায়া কেমনভাবে তাঁর দর্শনে প্ৰতিফলিত হয়েছে সে-কথা একটু পরে তোলা যাবে। তার আগে দেখা যাক থ্যালিসের জীবনী, দেখা যাক তখনকার প্রয়োগ প্ৰধান বিজ্ঞানের সঙ্গে আর কর্মজীবনের সঙ্গে তার কী-রকম গভীর যোগাযোগ।
অবশ্যই, থ্যালিসের কোনো পূর্ণাঙ্গ জীবনচরিত তখনকার দিনে কেউই লিখে যাননি। তবুও নানান প্রাচীন পুঁথিপত্র থেকে তাঁর জীবনী সম্বন্ধে কতকগুলো টুকরো কথা উদ্ধার করা যায়। আজকের ঐতিহাসিক মোটামুটি এরই ভিত্তিতে থ্যালিসের একটা জীবনচরিত গড়ে তোলবার চেষ্টা করেন। এই জীবনচিত্রের একটা প্ৰধান কথা হলো, তখনকার দিনে বিজ্ঞানের যতটুকু উন্নতি হয়েছিল তার সঙ্গে থ্যালিসের ঘনিষ্ঠ পরিচয়। অবশ্যই, থ্যালিসের আগে বিজ্ঞানের সত্যিই জন্ম হয়েছিল কি-না, তা তর্কের বিষয়; কেননা তাঁর আগে পর্যন্ত জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি ধর্ম ও পৌরাণিক বিশ্বাসের দখল থেকে মুক্তি পায়নি। তবু জ্যামিতিতে অগ্ৰণী ছিল মিশর, জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যাবিলোনিয়া, নৌবিদ্যায় গ্রীকদের চেয়েও বেশি নাম-ডাক ছিল ফিনিসীয় বণিকদের। খুব সম্ভব, ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষেই থ্যালিস মিশর দেশে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে তিনি শিখেছিলেন জ্যামিতি। কিন্তু মিশরবাসীরা এ-বিজ্ঞানের প্রয়োগ জানত শুধুই জমিজায়গা মাপ-জোখ করবার ব্যাপারে, বস্তুত এই কাজের দাবিই ওদের মধ্যে জ্যামিতি-বিজ্ঞানের জন্ম দিয়েছিল। থ্যালিস কিন্তু জ্যামিতির হিসেবা-নিকেশের উপর নির্ভর করে একটি উপায় বের করলেন, যে উপায়ের সাহায্যে সমুদ্রের বুকে জাহাজ কতখানি দূরে রয়েছে তা নির্ণয় করা সম্ভব। তাছাড়া, জ্যামিতিতে একটি কথা জানা হলো এক-জিনিস, কথাটাকে প্ৰমাণ করতে পারা আর এক-জিনিস। প্ৰমাণ করবার শর্তগুলি মিশরবাসীদের কাছে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েনি, ধরা পড়ল থ্যালিসের কাছে। যেমন ধরা যাক, মিশরবাসীরাও জানত একটা বৃত্তের (circle) ব্যাস (diameter) বৃত্তটিকে সমান দু’ভাগে বিভক্ত করে; কিন্তু এ কথাকে নিভুলভাবে প্রমাণ করতে তারা জানত না। প্রমাণ করবার পথ দেখালেন থ্যালিস। তাঁর এইরকম একটা কোনো কীর্তির কথা মনে রেখে আধুনিক যুগের দিকপাল দার্শনিক ইমানুয়েল কাণ্ট থ্যালিসকেই ইতিহাসের প্ৰথম প্ৰকৃত গণিত-বিজ্ঞানীর সম্মান দিতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি প্ৰথম গণিত-বিজ্ঞানী হোন আর নাই হোন, এ-কথায় কোন সন্দেহ নেই যে, থ্যালিস মিশর থেকে জ্যামিতি শুধু শিখেই আসেননি, জ্যামিতিকে আরো উন্নত করার ব্যাপারে তার অবদান ছিল অনেকখানি। ব্যাবিলোনবাসীদের জ্যোতির্বিজ্ঞানের বেলাতেও একই কথা। ওরা গ্ৰহনক্ষত্রের একটা ছক তৈরি করেছিল; সেই ছকের উপর নির্ভর করে ৫৮৫ খ্ৰীষ্টপূর্বাব্দে থ্যালিসই প্ৰথম হিসেব করে বলে দেন করে গ্ৰহণ হবে সেই দিনটির কথা। নৌবিদ্যায় আকাশের তারার উপর নির্ভর করে দিক নির্ণয়ের যে-কৌশল ব্যাবিলোনবাসীরা আয়ত্ত করেছিল, গ্ৰীক নৌবিদ্যায়। সেই কৌশল আমদানি করলেন থ্যালিস।
শুধু বিজ্ঞানের কথাই নয়। বিষয়বুদ্ধির দিক থেকেও তিনি রীতিমত ধুন্ধর ছিলেন। একবার কারা নাকি তাকে অকৰ্মণ্য বলে ঠাট্টা করেছিল, এতে তিনি বিলক্ষণ বিরক্ত হন এবং ঠিক করেন ব্যবসা-বুদ্ধি দেখিয়ে বণিকদেরও তাক লাগিয়ে দিতে হবে। এবং সে বছর জলপাই-তেলের ব্যবসা করে তিনি বিস্তর সম্পত্তি করে ফেললেন, দেখিয়ে দিলেন লক্ষ্মী-সরস্বতী উভয়কেই কেমন করে একসঙ্গে বশ করা যায়।
অবশ্য, প্ৰাচীন ইতিহাসে থ্যালিসের এত যে খ্যাতি, তা তাঁর বিষয়বুদ্ধির গুণেও নয়, জ্যামিতি-বিজ্ঞানে বুৎপত্তির দরুনও নয়। খ্যাতিটা হলো দার্শনিক প্ৰতিভার। তা-ও, দর্শন সম্বন্ধে তিনি এমন কিছু পুঁথিপত্র লিখে যাননি, অন্তত তাঁর লেখা কোনো পুঁথির কোনো খবর আমরা পাইনি। তার দার্শনিক প্ৰতিভার মাত্র একটি ভাঙা-চোরা টুকরো-মাত্র একটি কথা—সুদূর অতীত পেরিয়ে আমাদের কাছ পৰ্যন্ত পৌঁছেছে। তাছাড়া, আপাতদৃষ্টিতে, কথাটার মধ্যে দার্শনিক প্ৰতিভার এমন কিছু যুগান্তকারী স্বাক্ষর খুঁজে পাওয়া যায় না। কথাটা হলো : জল-ই পরম সত্তা, জল থেকেই সব কিছুর উৎপত্তি, জলের মধ্যে সব কিছু বিলীন হয়ে যায়। ভাবতে অবাক লাগে, শুধুমাত্র এইটুকু কথার জোরে খ্যালিস কেমনভাবে ইওরোপীয় দর্শনের আদিপুরুষ হিসেবে স্বীকৃত হন, বিশেষ কয়ে স্বীকৃতিটা যখন সৰ্ববাদিসম্মত। গ্ৰীক যুগে এ্যারিস্টটুল-এর যে গ্রন্থে গ্ৰীক-দৰ্শনের একটা ধারাবাহিক পরিচয় দেবার প্রথম চেষ্টা, সেই গ্ৰন্থ থেকে শুরু করে অতি-আধুনিক যুগে বার্টরাও রাসেল পাশ্চাত্ত্য দর্শনের যে ইতিহাস রচনা করেছেন, সেই ইতিহাস পর্যন্ত সর্বত্রই থ্যালিসের এই গৌরব।
অথচ, এমনিতে দেখলে কথাটার মধ্যে না আছে অভিনবত্ব, না যাথার্থ। অভিনবত্ব কোথায়? থ্যালিসের আগেও কবি হোমার এবং হেসইড, কল্পনা করেছিলেন জল থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হবার কথা, এমন-কী মিশর ও ব্যাবিলোনএর প্রাচীন পুরাণেও এ-জাতীয় কল্পনার স্বাক্ষর। ব্যাবিলোনের পুরাণে বলা হয়েছে, এককালে সব কিছু ছিল জল, শুধু জল; স্রষ্টা–যাঁর নাম কিনা মার্দুক–সেই আদি প্লাবন থেকে সৃষ্টি করলেন পৃথিবী।
তাহলে? থ্যালিসের আত যে গৌরব তা ঠিক কিসের দরুন? উত্তরে বলা হয়, জল থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হবার উপাখ্যানটা যদিও অতীতের পৌরাণিক কল্পনায় একাধিকবার উকি দিয়েছে, তবুও তা নেহাতই পৌরাণিক কল্পনা হিসেবে, ধর্মের অঙ্গ হিসেবে। আর তাই, সেগুলি দর্শনের মর্যাদা পাবার যোগ্য নয়। দর্শনের মর্যাদা প্ৰথম জুটল। থ্যালিসের, কেননা থ্যালিসই প্ৰথম পৌরাণিক চিন্তার কাঠামোটা পুরোপুরি বাদ দিয়ে, প্রকৃত বৈজ্ঞানিকের মেজাজ নিয়ে বিশ্বের রহস্য উদঘাটন করবার চেষ্টা করেছিলেন।
আসলে, জল থেকে সব কিছু সৃষ্টি হবার কথাটা, জলকে পরম সত্তা মনে করাটা বড় কথা নয়; এমন-কী ঠিক কথাও নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের কৃপায় আমরা তো স্পষ্টভাবেই জেনেছি জলকে পরম সত্তা বলাটা ভুল, জলের মূলে রয়েছে দু’ রকমের গ্যাস, সেগুলির মূলে রয়েছে আরো মৌলিক সত্য। তবু অতীতের কল্পনায় সৃষ্টিরহস্যের সঙ্গে জলের যোগাযোগ; কেননা মানুষের যে-সব প্ৰাচীনতম সভ্যতা, সেগুলি গড়ে উঠেছিল। সেকালের বড় বড় নদীর কিনারায়; মিশরের নীল নদ, ভারতের গঙ্গা আর সিন্ধু, ইরাকের ইউফ্রেটিস আর টাইগ্রিস, চীনের ইয়াং-সি-কিয়াং আর হোয়াং হো। তখনকার মানুষের চোখের সামনে তাদের ছোট্ট পৃথিবীটুকু—নদীর কিনারার ওই জায়গাগুলো মাঝে মাঝে জলের প্লাবনে মুছে যায়, তারপর আবার উর্বর পলিপড়া জমি জেগে ওঠে জলের নীচ থেকে। তাই তাদের কল্পনা ঘুরে ফিরে বার বার জলকেই সৃষ্টি-প্রলয়ের জন্যে দায়ী করতে চেয়েছে। কিন্তু বিশেষ করে মনে রাখা দরকারপ্ৰাচীনদের কল্পনায় শুধু জল নয়, জলের সঙ্গেই সৃষ্টিপ্রলয়ের এক অধিদেবতাও। জল থেকে সৃষ্টি, সৃষ্টি করেছেন এক আদি বিধাতা-পুরুষ। ব্যাবিলোনবাসীরা তার নাম দিয়েছিল মার্দুক; অন্য দেশে অন্য কোনো নাম।
থ্যালিসের যেটা আসল গৌরব, সেটা হলো এই “মাদুককে সরাসরি বাদ দেবার” গৌরব। (ফ্যারিংটন)। বিধাতা-পুরুষের কথা বাদ দিয়ে তিনি শুধু পার্থিব জিনিসের সাহায্যে পরম সত্তাকে চেনাবার চেষ্টা করেছিলেন। থ্যালিস ইওরোপের আদি-দার্শনিক, কেননা তিনিই প্ৰথম পৌরাণিক কল্পনাকে পিছনে ফেলে বিজ্ঞানের আলোয় বিশ্বব্রহস্যের কিনারা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর কথাটুকু আর যাই হোক, ধর্মবিশ্বাসের অঙ্গ নয়, নয় পৌরাণিক কল্পনার ক্রীতদাস।
মিশরের সভ্যতা, ব্যাবিলোনের সভ্যতা-গ্রীক সভ্যতার চেয়ে অনেক পুরানো। মিশরে আর ব্যাবিলোনে জ্যোতিষাদির জন্ম হয়েছিল, পণ্ডিতেরা চেষ্টা করেছিলেন বিশ্বের মূল রহস্যকে চেনবার বা বোঝবার; কিন্তু তবু মিশর বা ব্যাবিলোনে জন্ম হয়নি দর্শনের, জন্ম হলো গ্রীসে। গ্রীসেই প্ৰথম। কেননা, মিশর বা ব্যাবিলোনে বিশ্বরহস্যকে চেনবার চেষ্টাটা প্ৰকৃত বিজ্ঞানের আলোয় চেনবার চেষ্টা নয়, তার বদলে পৌরাণিক কুসংস্কারের পায়ে পায়ে ঘোরা, ধর্মবিশ্বাসের মোহ দিয়ে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাকে মেটাবার চেষ্টা। গ্রীসেই প্রথম তার হাত থেকে মুক্তি, স্বাধীন বুদ্ধি আর বিজ্ঞানের আলোয় পরম সত্যকে আবিষ্কার করার আয়োজন।
কিন্তু কেমন করে সম্ভব হলো এটা? এ কি শুধুই থ্যালিসের বাক্তিগত প্ৰতিভার ফল? কিংবা জাতি হিসাবে গ্ৰীক জাতি সত্যিই কি এমন কোনো আলোকসামান্য বৈশিষ্টের অধিকারী ছিল, যার কৃপায় এমনতর সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড সম্ভব হলো ওদের মধ্যে?
আসলে, ব্যক্তিগত প্ৰতিভা বা জাতিগত বৈশিষ্ট্য দিয়ে ঐতিহাসিক সমস্যার কিনারা করা যায় না। কেননা, তাতে শেষ পর্যন্ত কোনো-না-কোনোভাবে রহস্যকেই মেনে নিতে হয়। গ্রীকদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই ছিল, থালিসের নিশ্চয়ই ছিল অসামান্য প্ৰতিভা। কিন্তু প্রশ্ন হলো, গ্রীকদের এমনতর বৈশিষ্ট্য সম্ভব হলো কী করে? কী করে সম্ভব হলো থ্যালিসের এই প্ৰতিভা ঠিক এই পথে প্রবাহিত হওয়া? থ্যালিসের ব্যক্তিগত প্ৰতিভা তো প্রাচীন ধর্মমোহকে আরো মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করতেও পারত। আমাদের দেশের জনৈক চিন্তাশীলের সঙ্গে তুলনা করলে এই সম্ভাবনার কথাটা আরো স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যাবে। আচাৰ্য শঙ্করের ব্যক্তিগত প্ৰতিভাও তো খুবই অসামান্য। তবু, অতখানি প্ৰতিভার গতি কী হলো? ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের পায়ে আত্মনিবেদন : ধর্মমোহের পুরো কাঠামোকে নির্বিবাদে মেনে নিয়ে শ্রুতিস্মৃতির কথাগুলিকেই সবচেয়ে দুর্ধর্ষ যুক্তির ভিত্তিতে প্ৰতিষ্ঠা করার চেষ্টা! থ্যালিসের বেলায় মোটেই তা নয়। কেন নয়? এ-প্রশ্নের জবাব শুধু তার ব্যক্তিগত প্ৰতিভায় খুঁজে পাওয়া যায় না।
অবশ্যই, বিধাতার লীলাখেলা দিয়ে, তার খেয়ালখুশি বা আত্মবিকাশের একটা উপকথা সৃষ্টি করে পৃথিবীর সব সমস্যার একেবারে নিরাপদ আর নির্বিবাদ সমাধান নিশ্চয়ই করে দেওয়া যায়। ইতিহাস-বিচারে যেমনটা করে। থাকেন দার্শনিক হেগেলের ভক্তরা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সমাধান আমাদের বৈজ্ঞানিক বিবেককে কিছুতেই তুষ্ট করতে পারে না। পাকা ফলটা মাটির দিকে কেন পড়ল-এই প্রশ্নের উত্তরে নিশ্চয়ই বলা চলত; করুণাময়ের ইচ্ছে, তাই। কিন্তু উত্তরটা নিউটনের বৈজ্ঞানিক বিবেককে তুষ্ট করতে পারেনি। কেননা, বিজ্ঞান হলো বাস্তবপরায়ণ। বাস্তব দিয়ে ব্যাখ্যা না হলে আমাদের বৈজ্ঞানিক বিবেক কখনোই খুশি হতে পারে না। ইতিহাসের বেলাতেও একই কথা। কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার ব্যাখ্যা খুঁজতে হলে যতক্ষণ না বাস্তব বিষয় দিয়ে এই ব্যাখ্যা দেওয়া যায়, ততক্ষণ আমাদের বৈজ্ঞানিক চেতনা তুষ্ট হতে পারে না।
এই দাবির দরুনই সম্ভব হয়েছে ইতিহাসের বাস্তবপরায়ণ ব্যাখ্যা : ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকে বাস্তব পৃথিবীর বিষয় দিয়ে বোঝবার আয়োজন। কেমন করে সম্ভব হলো থ্যালিসের দর্শন? কেমন করে সম্ভব হলো পৌরাণিক, কল্পনাকে পিছনে ফেলে বিজ্ঞানের আলোয় বিশ্ব রহস্যের সমাধান খোজা? মিশর বা ব্যাবিলোনের প্রাচীনতম সভ্যতায় যা সম্ভব হয়নি, কেমন করে তা সম্ভব হলো গ্ৰীক সভ্যতায়?
এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাওয়া যাবে সমাজের গড়নের দিক থেকে।
মিশর প্রভৃতি প্ৰাচীনতর সভ্যতাগুলি গড়ে উঠেছিল। সেকালের বড় বড় নদীর কিনারায় কিনারায়। পলিপড়া উর্বর জমিতে খাদ্যের জোগান অনেক বেশি, তাই আদিম যাযাবর মানুষের দল এই সব জায়গাগুলিতেই ক্রমশ খিতিয়ে বসতে থাকে, গড়ে তোলে মানুষের প্রথম সভ্যতা। কিন্তু খাদ্যের জোগান বেশি হলেও জল সরবরাহের ব্যাপারে দারুণ সমস্যা : প্ৰকৃতিতে জলের যে সরবরাহ, শুধু তার উপর নির্ভর করা চলে না। বর্ষার সময় বৃষ্টির জল আর বন্যার জলে নদীর কিনারাগুলি একেবারে জলাভূমিতে পরিণত হয়ে যাবার ভয়, আবার বৃষ্টি বন্ধ হলে বা বন্যার জল সরে গেলে দারুণ জলকষ্টের ভয়। অথচ, জলই এই সভ্যতাগুলির প্রাণবস্তু, কেননা সভ্যতাগুলি প্ৰধানত চাষবাসের উপর নির্ভরশীল। তাই, মস্ত বড় সমস্যা হলো কৃত্রিম উপায়ে জলসেচের ব্যবস্থা করা, প্ৰকৃতিতে জলের যে খেয়ালী সরবরাহ তার উপর মানুষের দখল স্থাপন করবার সমস্যা। নদীতে বাধ বেঁধে বন্যার জল আটক রাখা, আবার খালি কেটে দরকার মতো এদিক-ওদিক জল সরবরাহ করা।
কৃত্রিম জলসেচ ব্যবস্থার দরুনই এই সভ্যতাগুলিতে ক্রমশ কেন্দ্রীয় সরকার গড়ে উঠতে লাগল। বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুসারে একই নদীতে নানান রকম বাঁধ বেঁধে নানান ধরনের জলসেচ ব্যবস্থা করতে গেলে তো চলে না, তাই দরকার পড়ল কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার, আর এই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার দায় গ্ৰহণ করার জন্যে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ। তার মানেই হলো কেন্দ্রীয় শাসক-তারই কবলে বিরাট বিরাট এলাকা। পুরো এলাকার সমস্ত মানুষের উপর যথেচ্ছাচার চালাবার ঢালাও সুযোগ। কোনো এলাকার মানুষ যদি কেন্দ্রীয় শাসকের মজিটা মানতে রাজি না হয়, তাহলে সেই এলাকার জল সরবরাহ বন্ধ করে তাদের অনায়াসেই জব্দ করে দেওয়া যাবে। কেন্দ্রীয় শাসকদের শক্তি তাই প্ৰায় অসীম। এই শক্তির কথাটা মনে না রাখলে বুঝতে পারা যায় না, সেই সুদূর অতীতের মানুষ কেমন করে গড়ে তুলতে পারল রুক্ষ মরুভূমির বুকে পিরামিডের মতো অবিশ্বাস্য বিশাল পাথরের গাঁথনি, বা পাহাড়ের চুড়োয় পাথর দিয়ে গাথা বিরাট মন্দির। তখনকার দিনে যান্ত্রিক কলাকৌশলের উন্নতি প্ৰায় নগণ্য, তাই এ-জাতীয় বিরাট কীতির মূল রহস্যটুকু খুঁজে পাওয়া সম্ভব শুধুমাত্র লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তজলকরা মেহনতের মধ্যে। কিন্তু অত লক্ষ মানুষকে অমন মূক পশুর মতো মেহনত করতে বাধ্য করা গেল কী করে? তার কারণ, বিরাট বিরাট এলাকার উপর, অসংখ্য মানুষের জীবনের উপর কেন্দ্রীয় শাসকের অসীম-অগাধ প্ৰতিপত্তি : সমস্ত এলাকার জল সরবরাহটি যার মজির উপর নির্ভর করছে, সে নিশ্চয়ই পুরো এলাকার মানুষকে মুখ বুজে মেহনত করবার জন্যে ঝোঁটিয়ে আনতে পারে। পুরো এলাকার প্রধান নির্ভর চাষবাস, চাষবাসের প্রধান নির্ভর জল সরবরাহ।
এই হলো আদিম সভ্যতাগুলির আসল চেহারা। এ সভ্যতায় জ্যোতিষ বা জ্যামিতির জন্ম সম্ভব, কিন্তু বিজ্ঞানের আলোয় বিশ্বরহস্যকে বোঝবার অবসর নেই। জমির মাপজোখ করবার কাজে দরকার জ্যামিতি, শুবু আদায়ের কাজে দরকার পাটীগণিত, দিনক্ষণ আর সন-তারিখের খেয়াল রাখবার কাজে দরকার জ্যোতির্বিদ্যা; এইরকম আরো কিছু কিছু। কিন্তু—আর এইটেই খুব বড় কথা–এ সভ্যতায় এই জাতীয় জ্ঞানের যে-রকম চাহিদা, সেইরকমই চাহিদা হলো ধর্মমোহের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখা। কেননা, এ-সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার জন্যে একান্ত দরকার ওই ধর্মমোহ, অন্ধ সংস্কার, পৌরাণিক বিশ্বাস। এ-সমাজ এমন সমাজ নয়, যেখানে সুস্থ বুদ্ধি দিয়ে, বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা দিয়ে বিশ্বরহস্যের সমাধান-প্ৰচেষ্টাকে উৎসাহ, এমন-কী আমল, দেওয়া সম্ভব; তাতে কেন্দ্রীয় শাসকের অসীম দাপটট ক্ষুব্ধ হবার ভয়, ভয় জনজাগরণের। “খ্ৰীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর এক মার্জিত গ্ৰীক চিন্তাশীল মিশরের শাসক-স্বীকৃত ধর্মের দিকে চেয়ে দেখছেন আর আবিষ্কার করছেন। এর সামাজিক প্রয়োজনীয়তা। তিনি বলছেন, মিশরের আইনকর্তা এত সব নোংরা কুসংস্কার সৃষ্টি করেছিল, তার কারণ প্রথমত, তার ধারণায় উপরওয়ালার যে-কোন আদেশ জনগণ যাতে স্বীকার করে নেয়। সেজন্যে তাদের অভ্যস্ত করা দরকার, আর দ্বিতীয়ত তার মনে হয়েছিল, যাদের মনে ধর্মভাব অন্যান্ত সব ব্যাপারে মনকে আইনের অনুগত করেছে তাদের উপর সহজে নির্ভর করা সম্ভব।”
তাই আদিম সামন্ত সভ্যতায় নিছক কৃষিকাজের তাগিদে যে-রকম কয়েকটি বিদ্যার দরকার, সেইরকমই দরকার হলো সংস্কারের, ধর্মমোহের। তাই বিশ্বের রহস্যটা পুরাণের আলোতেই বোঝবার সুযোগ, বিজ্ঞানের সঙ্গে তার মুখ দেখাদেখি নেই।
কিন্তু গ্রীকদের বেলায় অন্য রকম।
প্রথমত, গ্ৰীস-এর প্রাকৃতিক অবস্থাটা অন্য রকম। অনুর্বর দেশ। মিশর বা মেসোপটেমিয়ার বড় নদীর কিনারায় যে-রকম সহজে চাষবাস করা সম্ভব, গ্রীসের জমিতে বা গ্ৰীক উশনিবেশগুলির জমিতে মোটেই তা নয়। আর তাই গ্রীকদের মধ্যে শুরু থেকেই চাষ-বাসের চেয়ে পশুপালনের দিকেই ঝোক অনেক বেশি। তারপর, সওদাগরির দিকে ঝোক। এশিয়াটিক সামন্ত সভ্যতায় সওদাগর যে ছিল না, তা নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু সওদাগররা সভ্যতার সদর মহলে খুব বেশি প্রতিপত্তি পায়নি। তারা ছিল সামন্তদের আশ্ৰিত; নিজেদের যাতে আরো টাকাকড়ি জোটে, এই উদ্দেশ্যেই সামন্তরা সওদাগরদের কাজে লাগাত, একটু-আধটু প্রশ্ৰয়ও দিত। কিন্তু গ্ৰীক দেশে সওদাগরিটাই প্ৰধান হয়ে দাড়াল, আর তাই এখানে সওদাগর শ্রেণী বলে একটা আলাদা সামাজিক শ্ৰেণী গড়ে উঠতে লাগল। সওদাগরদের এই প্ৰতিপত্তির মূলেও আসল কারণ কিন্তু দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা : ওখানে পাহাড়ী জমিতে নানান রকম ধাতু, তাই দিয়ে নানান রকম জিনিস তৈরি করে রপ্তানি করবার সুযোগ। তাছাড়া, শ্বেতপাথর, কাঠ, জলপাই তেল, বাসন গড়বার জন্যে একরকম ভালো মাটি ইত্যাদি অনেক কিছুর জোগান। গ্রীসের মাটি অনুর্বর বলে যে-রকম চাষবাসের উন্নতি কম, সেইরকমই এই সব জিনিসের প্রচুর জোগান বলেই এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে ওঠবার ঢালাও সুযোগ,–আর তারই দরুন বণিক শ্রেণীর সামাজিক প্ৰতিপত্তি।
বণিক শ্রেণীর কথাটা ভালো করে বুঝতে হবে। গ্ৰীক সভ্যতায়, অন্তত গ্ৰীক সভ্যতার প্রথম দিকে, বণিক শ্রেণী বলতে নেহাতই পরিশ্রমজীবী মুনাফাখোর কোনো শ্রেণীকে নিশ্চয়ই বোঝাত না। এই শ্রেণী সামাজিক মেহনন্তের ক্ষেত্রে অংশ গ্ৰহণ করেছে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই। প্ৰকৃতিকে বেশি। করে, ভালো করে জয় করবার উপরই তাদের সম্পদ নির্ভর করেছে, আর প্ৰকৃতিকে জয় করবার যে কৌশল তারই নাম যে-হেতু বিজ্ঞান, সেইহেতু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে এই বণিক শ্রেণীর স্বাৰ্থ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জড়িত। তাছাড়া, মনে রাখতে হবে, গ্ৰীক সভ্যতার গোড়ার দিকে (“গ্রীক আদিযুগের শেষের দিকে”) অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে সাধারণ জনগণের যে-সংগ্ৰাম, সেই সংগ্রামে সওদাগর শ্রেণী জনগণের তরফে অধিনায়কত্ব করেছে। তাই তখন পৰ্যন্ত, সওদাগর শ্রেণী বলতে সামাজিক অর্থে নানান দিক থেকে এক প্ৰগতিশীল শ্রেণীকেই বোঝায়। অবশ্যই, গ্ৰীক সভ্যতার ভিত্তিতে দাস প্ৰথা : পয়সা দিয়ে মানুষ কিনে তাদের অমানুষিক পরিশ্রম করানো আর তাদের মেহনত দিয়ে তৈরি জিনিস মালিকদের ভঁড়ারে গেলবার ব্যবস্থা। দাসসমাজ,-পরিশ্রমজীবী সমাজই। কিন্তু, মনে রাখতে হবে, দাস-সমাজেরও একটা ইতিহাস আছে। গ্ৰীক সভ্যতার শুরু থেকেই দাস-সমাজের পরোপজীবী মূর্তি প্রকট হয়ে পড়েনি। দাস-প্রথার ইতিহাসকে মোটের উপর দুটো যুগে ভাগ করা যায়; প্রথম যুগটায় ক্রীতদাসদের শুধু গৃহস্থালির কাজে, অর্থাৎ চাকরিবাকির হিসাবে, নিয়োগ করা; অর্থাৎ সামাজিক মেহনন্তের যেটা প্ৰধান দায়িত্ব, সেটা তখন পর্যন্ত শুধু ক্রীতদাসদের কাধে চাপিয়ে দেবার ব্যবস্থা নয়। দ্বিতীয় যুগটায় দেখা দিয়েছে এই ব্যবস্থা, গ্রীকরা তখন নেহাতই পরশ্রমজীবী হয়ে দাঁড়িয়েছে।
গ্ৰীক দর্শনের ইতিহাস আলোচনায় দেখতে পাওয়া যায়, দাস-সমাজের প্ৰথম স্তরটা ছেড়ে যতই তারা দ্বিতীয় স্তরটার দিকে এগিয়েছে, ততই ওদের দর্শনে ফুটে উঠেছে শৌখিন চিন্তা-বিভোরতার লক্ষণ। কিন্তু থ্যালিস যে সময়টার দার্শনিক, যে সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে এবং যে সামাজিক শ্রেণীর সঙ্গে তার যোগাযোগ, তা দাস,সমাজের প্রথম দিককার কথা।
খ্ৰীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর আইয়োনিয়ায় তখন রাজনৈতিক শক্তি অনেকাংশেই এসেছে সওদাগর শ্রেণীর হাতে। এই সওদাগর শ্রেণী বিজ্ঞানের উন্নতি দিয়ে পৃথিবীকে আরো ভালো করে জয় করতে চায় এবং নিজেরাও অংশ গ্ৰহণ করে সামাজিক মেহনতে; দাসপ্রথা তখন এমন অবস্থায় পৌঁছয়নি যে, মেহনতজীবনকে ঘূণার চোখে দেখতে শেখার অভ্যাস। এই আইয়োনিয়ার সবচেয়ে কর্মমুখর শহর হলো মিলেটাস। সেই মিলেটাস শহরে সওদাগর শ্রেণীর একজন হলেন ইওরোপের প্রথম দার্শনিক, থ্যালিস। আর তাই তার কাছে ধর্মমোহটা প্রয়োজনীয় নয়, ধর্মমোহের চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন বিজ্ঞানের। আর তাই বিশ্বের রহস্য বোঝবার আশায় তিনি ধর্মমোহের দ্বারস্থ হতে রাজি নন, তার বদলে দ্বারস্থ হতে চাইলেন বিজ্ঞানের কাছে। ফলে বিশ্বের রহস্যবর্ণনায় স্ৰষ্টা মাদুক-এর স্থান রইল না। থ্যালিস বললেন, এই বাস্তব দুনিয়ারই একটি পদার্থ–জল, শুধু জল, আধ্যাত্মিক কোন কিছু নয়–পরম সত্য।
কর্মজীবনের সঙ্গে, বিজ্ঞানের সঙ্গে থ্যালিসের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগই তাকে বস্তুবাদী করে তুলেছিল, কিংবা, যা একই কথা, তার মনকে অধ্যাত্মবাদ বা ভাববাদের মোহ থেকে সরিয়ে আনল। এর দরুনই তার আদি-দার্শনিকের গৌরব। অবশ্যই তখনকার দিনে বিজ্ঞানের যতটুকু উন্নতি, তার ভিত্তিতে বস্তুজগতের পরম সত্তাকে সঠিকভাবে শনাক্ত করবার সম্ভাবনা নেই, থ্যালিস তা পারেননি,–থ্যালিসের কাছে তা আশা করবার কথাও নয়। তবু, যেটা আসলে অনেক বড় কথা, এইভাবে শনাক্ত করবার চেষ্টা দেখা দিল থ্যালিসের মধ্যে, এবং এই চেষ্টাই তাঁর পরে কিছুদিন পর্যন্ত গ্ৰীক দৰ্শনকে সঞ্জীবিত করে রেখেছিল।
থ্যালিসের পর এ্যানেক্সিমেণ্ডার, তার পর এ্যানেক্সিমেনিস। ঐতিহাসিকেরা বলেন, এ্যানেক্সিমেণ্ডার খুব সম্ভব। থ্যালিসের সমসাময়িক ছিলেন, কিংবা তার শিষ্য ছিলেন। এ্যানেক্সিমেণ্ডারের সঙ্গে এ্যানেক্সিমেনিসের সম্পর্কটাও এই রকমেরই। এরা দুজনেও ওই একই শহরের বাসিন্দা, একই সামাজিক পরিবেশের মানুষ। এবং দার্শনিক হিসাবে এদের দুজনের চেষ্টাও একই। রকম : বস্তুজগতের মধ্যেই পরম সত্তার প্ৰকৃত রূপকে শনাক্ত করবার চেষ্টা। এ্যানেক্সিমেণ্ডার “জল’ নামের স্থূল বস্তুকেই পরম বস্তু বলে মেনে নিতে রাজি নন। বস্তুজগতের মধ্যে তিনি এমন এক সুক্ষ্ম বস্তুকে পরম সত্তা মনে করতে চান, যার থেকে ক্ষিতি অপ, তেজ আদি সব রকম স্থূলভূত বা স্থূল বস্তুর উৎপত্তি। এই জাতীয় সূক্ষ্মভুত বা সূক্ষ্ম বস্তুর তিনি নাম দিলেন ‘অনন্ত, অসীম, অবৰ্ণনীয় বস্তু, যার থেকেই কালে সব কিছুর জন্ম এবং যার মধ্যেই কালে সব কিছু বিলীন হয়ে যায়। অর্থাৎ, তাঁর মতে, এক আদিম অবর্ণনীয় সূক্ষ্মভুতই পরম সত্তা। কেবল মনে রাখতে হবে, এই পরম সত্তাটি আধ্যাত্মিক কিছু নয়, নেহাতই বাস্তব জিনিস, জড় জগতের পদার্থ।
কিন্তু এই জাতীয় বস্তুকে পরম সত্তা বলতে গেলে কথাটা যেন বড় বেশি। ধোঁয়াটে হয়ে যায়। বস্তুবাদীর পক্ষে মূর্ত বস্তুর দিকে আকৃষ্ট হবার তাগিদ। রয়েছে। অথচ মূর্ত বস্তু হিসাবে ‘জল’-এর মতো একটা কিছুকে সব কিছুর মূল সত্তা বলে মেনে নেওয়াও যেন স্থূল কথা। এ্যানেক্সিমেনিস। তাই যেন দুয়ের মধ্যে মিল ঘটাবার চেষ্টা করে বললেন : “বায়ু হলো পরম পদার্থ। হাওয়া জিনিসটা মূর্ত, তবু সূক্ষ্ম। তা-ই। আর হাওয়া যে বস্তুজগতেরই জিনিস, অধ্যাত্মজগতের কিছু নয়, এ কথা তো স্পষ্ট কথা।
মোটের উপর বস্তুজগতের ঠিক কোন জিনিসটিকে পরম সত্তা হিসাবে এরা শনাক্ত করবার চেষ্টা করেছিলেন, সেইটা বড় কথা নয়। বড় কথা হলো এদের বস্তুবাদ, বিজ্ঞানের আলোয় বিশ্বব্রহস্যের সমাধান করবার চেষ্টা, পৌরাণিক চিন্তাধারা আর ধর্মমোহকে পিছনে ফেলে এগিয়ে আসবার আয়োজন।
সকলেই মিলেটাস শহরের বাসিন্দা বলে এদের দর্শনকে অনেক সময় মিলেসীয় দর্শন বলা হয়। আবার আইয়োনিয়ার নাম থেকে এঁদের দর্শনের নামকরণ হয়েছে আইয়োনীয় দর্শন। এই আইয়োনীয় দর্শনই ইওরোপীয় দর্শনের আদি পর্যায়। মনে রাখতে হবে, এ দর্শন বস্তুবাদী, বিজ্ঞান আর সামাজিক মেহনতের সঙ্গে সম্পর্কের জোরেই তা সম্ভব হয়েছিল।
০৭. দর্শনের ইতিহাস বিচার
দর্শনের ইতিহাস বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়, সামাজিক মেহনতের সঙ্গে দর্শনের সম্পর্ক যখন ঘনিষ্ঠ তখন দর্শনে প্ৰগতির চিহ্ন : সুস্থ আর বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের দিকে ঝোঁক। কিন্তু এ সম্পর্ক যখনই শিথিল হয়েছে, তখনই দর্শনে ফুটে উঠেছে প্রতিক্রিয়ার প্রতিটি লক্ষণ : অধ্যাত্মবাদ। আর রহস্যবাদ, বৈজ্ঞানিক মেজাজের বদলে ধামিক মেজাজ, বস্তুবাদের বদলে ভাববাদ। এমনটা না হয়ে উপায়ও নেই। কেননা, একমাত্র মেহনতের মধ্যে-প্ৰয়োগজীবনের মধ্যে-হৃদয়ঙ্গম হয় বহির্বস্তুর অবধারিত যাথার্থ। কামারশালে লোহা পেটবার সময় কামার বোঝে-হাড়ে হাড়ে বোঝে—লোহা জিনিসটা স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মতিভ্রুমও নয়। তার বদলে এক ধরনের সত্যি জিনিস, যার বাস্তবতা দুর্ধর্ষ। তাই সমাজের সদর মহল থেকে মেহনতের সবটুকু ইজ্জত যদি মুছে যায়, তাহলে সেই মহলের চেতনায় বহির্জগতের এই যাথার্থ কীসের নির্ভরে টিকে থাকবে? মানুষের যে-হাত দুনিয়ার সঙ্গে সংগ্রামে প্ৰবৃত্ত সেই হাত যখন চোখের আড়ালে পড়ল, তখন যে-দুনিয়ার সঙ্গে সংগ্রাম সেই-দুনিয়ার কথাটাও ঝাপসা হয়ে আসবে না কি? বাকি থাকবে শুধু চেতনা–শুধু নিৰ্মল, নিরাবলম্ব, বিশুদ্ধ চেতনা। কেননা, মাথার ঘাম পায়ে ফেলবার তাগিদযখন নেই, তখন শুধুই মাথা-ঘামানো, তারই নাম হলো চেতনা। আর তাই, তখন মানুষের মনে এ-অভিমান জাগাই খুব স্বাভাবিক যে তার এই চেতনা বুঝি সর্বশক্তিমান, সর্বশক্তির আধার। এই অভিমানটাই হলো চেতনকারণবাদ বা অধ্যাত্মবাদ বা ভাববাদের আসল ভিত্তি।
য়ুরোপীয় দর্শনে যাঁরা আদি-দার্শনিক বলে স্বীকৃত, ইতিহাসে ধাদের নামকরণ হয়েছে আইওনীয় দার্শনিক, তঁদের বেলায় সামাজিক মেহনতের সঙ্গে দর্শনের সম্পর্কটা ঘনিষ্ঠ। তাই তাদের মেজাজ চোদে আনাই বৈজ্ঞানিকের মেজাজ, তঁদের দর্শনে সুস্থ বস্তুবাদের স্পষ্ট স্বাক্ষর,-ষদিও অবশ্য উপসংহারের দিক থেকে তঁদের বক্তব্যটুকু আজকের বৈজ্ঞানিক উপসংহারের তুলনায় অনেক স্থূল, অনেক প্ৰাকৃত।
আইওনীয়দের পর পিথাগোরাস, কিংবা আরো নিখুঁতভাবে বললে বলা উচিত পিথাগোর-পন্থীদের দল। কেননা এই দলের যিনি গুরুদেবঅর্থাৎ খোদ পিথাগোরাস-তিনি নিজে কোনো দার্শনিক গ্ৰন্থরচনা করেননি, এবং গ্রীক ঐতিহ্য অনুসারে এ দর্শনের উক্তিগুলি পিথাগোর-পন্থীদের উক্তি বলেই উল্লিখিত হয়েছে। যেমন ধরা যায়। এ্যারিস্টটুল-এর কথা। তার গ্রন্থে পূর্বদার্শনিকদের বর্ণনা করবার সময় তিনি কোনো কথাকেই পিথাগোরাসের একার কথা বলে উল্লেখ করেননি, বারবার উল্লেখ করছেন পিথাগোরপন্থীদের কথা হিসেবে। তবু পিথাগোরাসের ব্যক্তিগত প্ৰতিভা নিশ্চয়ই অসামান্য ছিল, দর্শনের ঐতিহাসিকেরা প্ৰায় একবাক্যে স্বীকার করেন, প্রাচীন ইতিহাসে এমনতর প্রতিভার নমুনা অত্যন্ত বিরল। অথচ, পিথাগোরাসের জীবনচরিত বলতে মাত্র দু’চারটে টুকরো কথা টিকে রয়েছে। সামস দ্বীপে তার জন্ম, কিন্তু ওখানে পলিক্রিটিসের শাসন অসহ জ্ঞান করায় তিনি ৫৩৫ খ্ৰীষ্টপূর্বাব্দে দক্ষিণ ইতালিতে গিয়ে আশ্রয় গ্ৰহণ করেন। অনুমান, তখন তার বয়েস বছর চল্লিশ। দক্ষিণ ইতালিতে ক্রোটন নামের জায়গায় তিনি তাঁর মঠ স্থাপন করেন, এবং ক্রমশ গড়ে ওঠে এ-মঠের নানান শাখা। মনে রাখতে হবে, পিথাগোর-পন্থীদের মঠ শুধুমাত্ৰ সাধন ভজন বা দার্শনিক ধ্যানধারণার কেন্দ্র ছিল না, ছিল ওঁদের বিশিষ্ট রাজনীতির ঘাঁটিও। ফলে, তাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীও ছিল। এবং এই প্ৰতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে সংঘর্ষের দরুনই বৃদ্ধ পিথাগোরাস শেষ পর্যন্ত প্ৰাণ নিয়ে মেটপন্টিয়ন্-এ পলায়ন করেন; সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁর ওই মঠ এবং মঠের বহু শাখা ধ্বংস করেছিল, এমন-কী খুন করেছিল তাঁর বহু শিষ্যকেও। পিথাগোরাসের জীবন সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য মোটের ওপর এইটুকুই। আরো কিছুটা আন্দাজ করা সম্ভব তাঁর দার্শনিক মতবাদের বিশ্লেষণ থেকে।
দর্শন হিসেবে, পিথাগোর-পন্থীদের দর্শনে প্ৰতিক্রিয়ার প্রায় প্রতিটি লক্ষণ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে; রহস্যবাদ। আর অধ্যাত্মবাদ, বস্তুবাদ ছেড়ে ভাববাদ, স্বাস্থ বিজ্ঞানের পথ ছেড়ে ধর্মমোহের পথ। তাই আইওনীয়দের তুলনায় এক আমূল পরিবর্তন। দর্শনের ইতিহাসকে বুঝতে হলে এই পরিবর্তনের একটা ব্যাখ্যা পাওয়া চাই। য়ুরোপীয় দর্শনের যে-সব সাবেকী ইতিহাস, সেই সব ইতিহাসে এই পরিবর্তনের প্রকৃত গুরুত্ব অনুভূত হয়েছে কি না, তা-ই সন্দেহের কথা। অথচ পরিবর্তনটা যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা শুধু একটা ব্যাপার থেকেই আন্দাজ করা যায়। এখান থেকে গ্ৰীক চিন্তাধারায় যে সংকট দেখা দিল, তার পরিণামে গ্ৰীক যুগের যিনি সবচেয়ে দিকপাল দার্শনিক বলে সাধারণত স্বীকৃত হন-অর্থাৎ প্লেটো-তার দর্শনে প্ৰতিক্রিয়ার সবচেয়ে চরম চিহ্ন। দ্বিতীয়ত, দর্শনের সাবেকী ইতিহাসগুলিতে এই পরিবর্তনের যেটুকু বা ব্যাখ্যা, তাও মোটেই সন্তোষজনক নয়। ব্যাখ্যাটা মোটের উপর দুরকমের। এক রকমের ব্যাখ্যা হলো, নিছক মজি-রুচির দিক থেকে ব্যাখ্যা; পিথাগোরাসের মজি ও রুচি অন্য রকমের ছিল, তাই তাঁর দর্শনটাও অন্য রকমের। অথচ, এটা তো কোনো ব্যাখ্যাই নয়, মূল সমস্যার বর্ণনামাত্র। কেননা আসল সমস্যা হলো; একটা বিশেষ যুগে চিন্তাশীলেরমর্জি-রূচিতে আমন আমূল পরিবর্তন দেখা দেয় কেমন করে? দার্শনিককে নিছক খেয়ালখুশির কারবারি মনে করলেও তার খেয়ালখুশির রকম-ফেরকে কোনো একটা নিয়ম দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করতে হবে তো, তা নইলে যে পাগলা ঘোড়ার পাগলামির সঙ্গে দার্শনিক যুগপরিবর্তনের কোনো তফাত থাকে না।
দর্শনের সাবেক ইতিহাসগুলিতে আর একরকম ব্যাখ্যা হলো হেগেলপখীদের ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যা অনুসারে, সব কিছুই লীলাময়ের লীলা, পরব্রহ্মের আত্মবিকাশ। সে আত্মবিকাশের অবশ্য একটা নিয়ম আছে, ক্ৰম আছে। দর্শনের ইতিহাসে যে ক্ৰমবিকাশ, তা এই নিয়মেরই প্ৰতিবিম্বমাত্র। হেগেলপন্থীরা বলেন, প্ৰথম স্তরে লীলাময় নিজেকে বিকশিত করেন স্থূল ও মূর্ত বহির্বস্তু হিসেবে, তার পর ক্রমশ সূক্ষ্মর দিকে, চিন্মেয়ের দিকে অগ্ৰগতি। তাই, দার্শনিক চেতনার আদিতেও স্থূল ও মূর্ত বহির্বস্তুকে পরমসত্য বলে চেনবার প্রয়াস : আইওনীয় দার্শনিকেরা কেউ বা জলকে, কেউ বা পদার্থের প্ৰাকৃত প্ৰলয়কে, কেউ আবার বায়ুকে পরম সত্যের সম্মান দিতে চাইলেন। কিন্তু জলই হোক আর বায়ুই হোক, মনে রাখতে হবে সব কিছুই স্থূল বহির্বস্তু, জড়। দ্বিতীয় যুগটায়, হেগেল-পন্থীদের মতে, মানুষের দার্শনিক চেতনা আর এক ধাপ এগিয়ে এল। বস্তুজগৎকে, জড়কে একেবারে বর্জন করা যদিও সম্ভব হলো না, তবুও বস্তুজগতের স্থূল ও মূর্ত রূপটাকেই একমাত্র সত্য বলে মেনে নেওয়াও নয়। তার বদলে, বস্তুজগতের সূক্ষ্ম, অমূর্ত গঠনের দিকটাকেতার গাণিতিক লক্ষণকে-পরম সত্য বলে চেনবার প্রয়াস। জড়কে ছেড়ে আসা, যদিও কিনা জড়ের উপরে খানিকটা নোঙর থেকে গিয়েছে। হেগেলীয়দের এই ব্যাখ্যাটা প্ৰথমে স্পষ্টভাবে বোঝবার চেষ্টা করা হোক, তারপর দেখা যাক ব্যাখ্যা হিসেবে এটা কতখানি টিঁকসই।
পিথাগোর-পন্থীরা বলতেন, সংখ্যাই পরম সত্তা। এমনিতে কথাটার তাৎপৰ্য বোঝা কঠিন। কিন্তু হেগেলীয়রা বলেন, “সংখ্যা” বলে ব্যাপারটা যে আসলে কী, তা মনে রাখলে এই কথার একটা মানে খুঁজে পাওয়া যাবে। কেননা, “সংখ্যা” হলো বস্তুর অমূর্ত আর গাণিতিক রূপমাত্ৰ : ইন্দ্ৰিয় দিয়ে তাকে জানা যায় না, বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয়। ইন্দ্ৰিয় দিয়ে যেটুকু জানা যায় সেটুকু বস্তুর নেহাত স্থূল, নেহাত জড়রূপ। যেমন ধরা যাক, পাঁচটা বলদের কথা। রক্তমাংসে গড়া বলদের শরীরগুলোকে আমরা চোখে দেখতে পাই, হাত দিয়ে স্পর্শ করতে পারি,-অর্থাৎ জানতে পারি। ইন্দ্ৰিয়র সাহায্যে। কিন্তু রক্তমাংসে গড় শরীরগুলো তো নেহাতই স্থূল, নেহাতই জড়জিনিস। এছাড়াও কিন্তু পাঁচটা বলদের ব্যাপারে। আর একটা দিক রয়েছে,-সেইটাই হলো। গাণিতিক দিক, যার নাম ওই “সংখ্যা”। ওই “পাচ” বলে ব্যাপারটা। পাঁচটা বলদ আমরা চোখে দেখতে পাই, কিন্তু “পাঁচ” বলে–নিছক “পাঁচ” বলে–কোনো কিছুকে আমরা ইন্দ্ৰিয় দিয়ে জানতে পারি না। সংখ্যা তাই বস্তুর অমূর্ত গাণিতিক রূপ; একে বুদ্ধি দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করা যায়-এই রূপটা নিয়ে হিসেব করা যায়—ইন্দ্রিয় দিয়ে একে ধরাছোঁয়া সম্ভব নয়। পিথাগোর-পন্থীরা যখন এই “সংখ্যা”কে পরম সত্য বলে ঘোষণা করেন, তখন বুঝতে হবে তঁরা বস্তুর মূর্ত ও বাহরূপটাকে ছেড়ে তার অমূর্ত ও বুদ্ধিগ্রন্থ রূপটাকেই একমাত্র সত্য মনে করতে চেয়েছেন, অর্থাৎ চেয়েছেন চিন্ময়ের দিকে–চেতনকারণের দিকে–একধাপ এগিয়ে যেতে।
এই হলো হেগেল-পন্থীদের ব্যাখ্যা। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বুঝতে পারা যায়, এ-ব্যাখ্যা আসলে কোনো ব্যাখ্যাই নয়; ব্যাখ্যার বদলে একটি বিশিষ্ট দার্শনিক মতবাদের উল্লেখমাত্র। পরব্রহ্মের লীলাখেলা নিয়ে এক বিশিষ্ট দার্শনিক মতবাদ এবং সেই মতবাদকে প্রতিষ্ঠা করবার আশায় দর্শনের ইতিহাসকে বিশেষ একরকমভাবে মোচড় দেবার প্রচেষ্টা। অবশ্যই হেগেলের প্রতিভা ছিল অসামান্য, মানব ইতিহাসের প্রায় সমস্ত অভিব্যক্তিকেই লীলাময়ের অধ্যাত্মারস দিয়ে জীৰ্ণ করে নেবার দুর্লভ মেধা। কিন্তু এ-মেধা যতই অসামান্য হোক না কেন, হেগেল বা হেগেলা-পন্থীদের রচনা থেকে এই দার্শনিক হাওয়াবদলের কোন প্রকৃত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না; পাওয়া যায়। তার বদলে নিজেদের বিশিষ্ট দার্শনিক মতবাদ প্ৰতিষ্ঠা করবার পরিচয়।
আইওনীয় বস্তুবাদের পর পিথাগোরীয় অধ্যাত্মবাদ–দর্শনের এই দিকবদলাটুকুর বাস্তব ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া সম্ভব একমাত্র সামাজিক মেহনতের পটভূমিটা মনে রাখলে।
গ্ৰীক সমাজ ছিল দাস-সমাজ। তার মানে মেহনতের দায়টা ক্রীতদাসের উপর। কিন্তু দাস-সমাজেরও একটা ইতিহাস আছে। সে-ইতিহাসকে দুটি মোটা পৰ্যায়ে ভাগ করা চলে। প্রথম পর্যায়ে ক্রীতদাসুরা প্রধানতই গৃহস্থালির কাজে নিযুক্ত, কিন্তু সামাজিকভাবে মেহনতের পুরো দায়টা তখনো শুধু ক্রীতদাসের ঘাড়ে দেওয়া হয়নি। সামাজিকভাবে মেহনতের দায় বলতে বোঝায় পশুপালন, কারুশিল্প আর বিশেষ করে সওদাগরির জন্যে প্রয়োজনীয় মেহনত; কেননা গ্রীস দেশ রুক্ষ অনুর্বর দেশ, তাই চাষবাসের বদলে এইঃগুলির উপরই অনেক বেশি নির্ভরতা। তার মানে, দাস-সমাজের প্রথম পৰ্যায়ে ঘরকান্নার কাজকর্মের জন্যে যে-মেহনত দরকার, বিশেষ করে সেই মেহনতের দায়টা ক্রীতদাসের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার ব্যবস্থা। কিন্তু পশুপালন, কারুশিল্প আর বিশেষ করে সওদাগরির জন্যে যে-মেহনতের দরকার, তার পুরো দায়টা ক্রীতদাসের উপর নয়, সেখানে স্বাধীন গ্রীকদের নিজেদের মেহনতও। তাই এই যুগটায় গ্ৰীকসভ্যতার সদর মহল সামাজিক মেহনতের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েনি। ফলে দর্শন আর দার্শনিকের সঙ্গে তখনো সামাজিক মেহনতের যোগাযোগ। গ্ৰীক সওদাগরদের তখন সবচেয়ে বড়ঘাট হলো মিলেটাস শহর; কর্মমুখর এই শহরেই জন্ম হলো গ্ৰীকদর্শনের, আর গ্রীক দর্শনে যিনি আদিদার্শনিক তিনি কর্মজীবনের সাফল্যেই প্ৰাচীন যুগে সপ্তজ্ঞানীর এক জ্ঞানী বলে স্বীকৃত। কিন্তু দাস-সমাজের দ্বিতীয় পৰ্যায়ে মোটেই তা নয়; তখন থেকে যতখানি মেহনতের উপর পুরো সমাজটার নির্ভর, তার সবটুকুর দায়ই ক্রীতদাসের উপর। ফলে মেহনত পড়ল চোখের আড়ালে-কিংবা যা একই কথা, সমাজের সদর মহলের সঙ্গে মেহনতের সম্পর্ক হলো শিথিল। আর দর্শন বলে ব্যাপারটা যে-হেতু সমাজের সদরমহলেরই কীর্তি, সেইহেতু দাস-সমাজের দ্বিতীয় পৰ্যায়ে দর্শনের সঙ্গে সামাজিক মেহনতের আর সম্পর্ক রইল না।
পিথাগোরপন্থীদের দর্শন যখন পূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে, তখন দাস সমাজের এই দ্বিতীয় পৰ্যায়। মেহনতকারী বলতে শুধুই ক্রীতদাস, অর্থাৎ একধরনের ইতর জীব। তাই মেহনত বলে ব্যাপারটাই ইতরের ধর্ম। পিথাগোর-পন্থীদের দর্শনে এই মনোভাবের স্পষ্ট পরিচয়। ওঁরা বলেন, অলিম্পিক খেলার মাঠে যে-সব আগন্তুকদের জমায়েত, তাদের দিকে একবার চেয়ে দেখুন, দেখবেন। মোটের ওপর তিন ধরনের মানুষ; কেউ বা এসেছে খেলার মাঠে কেনা-বেচা করতে, কেউ বা এসেছে প্ৰতিযোগিতায় যোগ দিতে, আর কেউ বা নিছক দ্রষ্টা, এসেছে শুধু দেখতে-কিন্তু দেখা ছাড়া কোনোরকম গতির খাটানোর মধ্যে তারা নেই। এদের মধ্যে যারা এসেছে কেনা-বেচার উদ্দেশে তারাই হলো সবচেয়ে অধম, সবচেয়ে নীচু স্তরের মানুষ। তারপর তারা, যারা প্ৰতিযোগিতায় যোগ দিতে চায়। আর যারা দ্রষ্টা, নিছক দ্রষ্টা–শুধু দেখবে, কিন্তু কোনোরকম মেহনতোরই ধারকাছ ঘেঁষবে না।–তারাই হলো সবচেয়ে সেরা ধরনের মানুষ। পিথাগোয়-পন্থীরা বলেন, এই উপমাটা মাথায় রেখে সাধারণভাবে মানবসমাজকেও বোঝবার চেষ্টা করতে হবে। তার মানে, সাধারণ মানুষকেও তিনভাগে ভাগ করা দরকার; সবচেয়ে সেরা ধরনের মানুষ হলো তারাই, যারা শুধু দ্রষ্টা, যারা ভালোবাসে শুধু নির্মল নির্লিপ্ত জ্ঞান, লাভ-লোকসানের দিকে তাদের নজর নেই, তারা নয়। যশপ্ৰাৰ্থী, তারা তাই কোনোরকম মেহনতেরই ধার ধারে না। তারপর তারা যারা গতির খাটায় যশোর আশায়, অলিম্পিক জমায়েতে খেলোয়াড়দের মতো। আর সবচেয়ে নিচু স্তরের মানুষ-সব চেয়ে হীন-সবচেয়ে অধ্যম-হলো মেহনতকারী, অর্থাৎ যারা গতির খাটায় নগদ বিদায়ের মুখ চেয়ে, অলিম্পিক খেলার মাঠে পসারীদের মতো। এইখানে মনে রাখতে হবে, বেচা-কেনায় উৎসাহী ব্যবসাদার বলতে আমরা আজকাল যে-ধরনের মানে বুঝি, গ্ৰীক সমাজে ঠিক সেই ধরনের নয়। ও-সমাজের একটা প্ৰধান নির্ভর ছিল ব্যবসাদারি। আর সওদাগরি, তাই বেচা-কেনা বলে ব্যাপারটা সামাজিক মেহনতের মস্ত বড় দিকই।
মানুষের দলকে এই যে তিন ভাগে ভাগ করবার চেষ্টা, এর থেকেই বুঝতে পারা যায় পিথাগোর-পন্থীদের কাছে মেহনতের মূল্য কতখানি তুচ্ছ-কতটা হীন-হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর তারই পাশে নিছক নির্লিপ্ত জ্ঞানচর্চার গৌরবটা কী অসামান্য গৌরবে পরিণত হয়েছে। দাস-সমাজের প্রথম পৰ্যায়ে এমনটা হয়নি, এমনটা হবার কথা ময়। কেননা, তখন পৰ্যন্ত সমাজের যারা মাথা, তারা শুধুই মাথা খাটান না, মাথার ঘাম পায়ে ফেলতেও জানেন। কারুশিল্পে, ব্যবসায়, বাণিজ্যে নানান দিকে। কিন্তু দাস-সমাজের দ্বিতীয় পৰ্যায়ে আর তা নয়; তখন থেকে মেহনতের চিহ্নই ইতর মানুষের চিহ্ন।
ফলে, পিথাগোর-পন্থীদের পক্ষে মেহনতজীবনের ছোয়াচ বঁচিয়ে নির্জনে নির্লিপ্ত জ্ঞানের চর্চাকেই পরম পুরুষাৰ্থ মনে করা স্বাভাবিকু। তাই মঠ প্ৰতিষ্ঠা, দার্শনিকদের মঠ। স্বতন্ত্র দার্শনিক গোষ্ঠী গড়বার চেষ্টা আইওনীয়দের মধ্যে ছিল না, পিথাগোরদেরই প্ৰথম। এ-চেষ্টাকে তাদের খাপছাড়া খামখেয়ালের পরিচয় মনে করলেও ভুল করা হবে। এটা আসলে মেহনতকারী জনতা সম্বন্ধে তাদের বিতৃষ্ণ মেজাজেরই পরিণামমাত্র। নিকৃষ্ট মানুষের প্রবেশ নেই এই মঠে, এখানে শুধু নিৰ্বাচিত কয়েকজন নির্মল জ্ঞানচর্চায় বিভোর হয়ে দিন কাটাবেন। অবশ্যই বিশ্বের চরম রহস্য নিয়ে তাঁরা কী কিনারা করলেন-না করলেন, তা সাধারণ মানুষকে বুঝিয়ে বলবার তাগিদ থাকবার কথা নয়; পিথাগোর-পন্থীদের মধ্যে তা ছিল ও না। বরং তাগিদটা উলটো ধরনেরই; জনগণের কাছ থেকে জ্ঞানের কথাটা গোপন করা, লুকিয়ে রাখা। তাই তাদের ভাষাটাও দুৰ্বোধ্য, সংকেতময়, রহস্যঘন। তারা ওইরকম অদ্ভুত দুৰ্বোধ্য ভাষায় নিজেদের চিন্তাধারাটুকু নিছক নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন বলেই আধুনিক ঐতিহাসিক অনেক চেষ্টা করেও পিথাগোরপন্থীদের বক্তব্যটার পুরো অর্থ উদ্ধার করতে পারেন না, এবং শেষপর্যন্ত যেন হাল ছেড়ে বললেন : “এখানে শুধু দার্শনিক চিত্তাকর্ষণ নয়, এমন-কী ঐতিহাসিক চিত্তাকর্ষণও যেন উপে যায়” (সোয়োগলার)। যেমন ধরুন, ওদের মধ্যে কেউ বা বলছেন “ন্যায়= ৪”, কেউ বা বলছেন “ন্যায় = ৯”;–কিন্তু ৪-ই হোক আর ৯-ই হোক, এ-সব কথার যে কী মানে, আজকের দিনে তা আমাদের পক্ষে উদ্ধার করা সম্ভবই নয়। পাটীগণিতের মুখোশ পরানো এই রহস্যবাদের অর্থ আমরা কীসের ভিত্তিতে আন্দাজ করতে পারি?
দুৰ্বোধ্য সাংকেতিক ভাষায় নির্জনে চিন্তার জাল বোনা। কিন্তু মঠগুলো শুধুমাত্র দার্শনিক চিন্তার কেন্দ্র নয়। রাজনীতির ঘাটিও। পিথাগোরাসের একটা রাজনৈতিক মতবাদও ছিল, খুব সম্ভব সংগঠনও ছিল। মঠগুলো তারও কেন্দ্র। অবশ্য এই রাজনৈতিক মতবাদটা ঠিক কেমনতর, তার সুনিশ্চিত নির্দেশ পাবার উপায় নেই, আধুনিক পণ্ডিতেরা নানান রকম অনুমানের ভিত্তিতে পিথাগোর-পন্থীদের রাজনৈতিক মতবাদটা আন্দাজ করতে চান। এবং এ নিয়ে আধুনিক পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেউ বা মনে করেন, এই মতবাদটা ছিল সন্ত্রান্ত-তন্ত্র; মুষ্টিমেয় সম্রান্তের শাসনই সবচেয়ে ভালো। আবার কেউবা দেখাতে চেয়েছেন, পিথাগোর-পন্থীদের রাজনীতিটা ছিল গণতন্ত্র, সন্ত্রান্ত জমিদার-শ্রেণীর বিরুদ্ধে তাদের রাজনৈতিক সংগ্ৰাম।
অবশ্যই উভয় পক্ষের সিদ্ধান্তই ক্ষীণ ও ভঙ্গুর প্রমাণকে আশ্রয় করতে চায়; ধারা বলতেন পিথাগোর-পন্থীরা সম্রাপ্ত-পন্থী। আর যারা বলেন পিথাগোর-পন্থীরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী, তাদের উভয়েরই সপক্ষে ঐতিহাসিক সাক্ষ্য অত্যন্ত দুর্বল। তবু, পিথাগোর-পন্থীদের রাজনীতিতে প্ৰগতির চিহ্ন খোঁজবার চেষ্টাটা মোটের উপর বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ বলেই মনে হয়। যাদের চিন্তাধারায় এবং জীবনাদর্শে প্ৰতিক্রিয়ার প্রতিটি চিহ্ন এমন প্ৰকট, তাদের রাজনৈতিক মতবাদে প্রগতির পরিচয় থাকবার কথা নয়। তাছাড়া, যদিই বা টুকরোটাকরা কিছু কিছু সূত্র থেকে অনুমান করা যায় পিথাগোর-পন্থীদের রাজনীতিতে গণতন্ত্রের দিকে ঝোঁক, তবুও মনে রাখতে হবে, এ-গণতন্ত্র সমন্ত মানুষ সম্বন্ধে প্ৰযোজ্য হতেই পারে না। সমাজের ভিত্তিতে দাস-প্ৰথা, চুড়ায় সম্রান্ত তন্ত্র আর গণতন্ত্রের দ্বন্দ্ব। তাই গণতন্ত্রই হোক আর সামন্ততন্ত্রই হোক, শাসন-কাজে ইতর মানুষের, ক্রীতদাসের কোনো অধিকার নেই। তাই, সামাজিক মেহনতের সঙ্গে পিথাগোরপন্থীদের ঠিক কেমনতর সম্পর্ক ছিল-এ-প্রশ্নের আলোচনায় তাঁদের রাজনৈতিক মতবাদটা নিছক রাজনীতির পরিভাষায় সন্ত্রান্ততান্ত্রিক না। গণতান্ত্রিক, তার হদিশ খুব বেশি আলোকপাত করতে পারবে না। পুরো সমাজের গড়নটা তখন কী-রকম, তারই মীমাংসা এই মূল প্রশ্নের উত্তর নির্ণয় করবে। মনে রাখতে হবে, পুরো সমাজের জন্যে যতখানি মেহনত দরকার তার সবটুকুর দায়ই তখন শুধু ক্রীতদাসের ঘাড়ে, তাই সামাজিক মেহনতের চিহ্নটা ইতরের চিহ্ন, মেহনতকারীরা ইতর মানুষমাত্র। পিথাগোরীয় দর্শনে এই মনোভাবের স্পষ্টতম পরিচয়।
সামাজিক মেহনত থেকে পিথাগোর-পন্থীরা কী-ভাবে যে হিটে গিয়েছিলেন, তার আরো একটা জরুরি প্রমাণ এখানে উল্লেখ করা যায়। তঁদের আগে পৰ্যন্ত-অর্থাৎ আইওনীয় দার্শনিকদের বেলায়-দার্শনিক উপমা, এমন-কী দার্শনিক চিন্তাধারার মূল কাঠামোটুকুও সংগ্ৰহ করা হতো। দৈনন্দিন কর্মজীবনের দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ রেখে। অধ্যাপক ফ্যারিংটন দেখিয়েছেন, কেমনভাবে কুমোরের চাকা বা কামারের হাপর বা ওইরকম আরো পাঁচ রকম জিনিস থেকে গ্ৰীক যুগের আদি দার্শনিকেরা সংগ্ৰহ করতেন। চিন্তাধারার কয়েকটি মূল কাঠামো, এবং তাদের বেলায় এই ধারণাগুলি দিয়েই বিশ্বের পুরো রূপটাকে চেনবার চেষ্টা। কিন্তু পিথাগোয়-পন্থীদের বেলায় একেবারেই তা নয়। কর্মজীবনে হাতিয়ারগুলির কাছ থেকে চিন্তার কাঠামো সংগ্ৰহ করা নয়, তার বদলে সংগীতের কাছ থেকে। সংগীতের দিকে পিথাগোর-পন্থীদের নানামুখী ঝোঁক। তারা মনে করতেন সংগীতের সাহায্যে আত্মাকে সংস্কৃত আর ক্লেদমুক্ত করা সম্ভব। তখনকার কালে কোরিবাস্তিক পুরোহিতেরা সংগীতের সাহায্যে-বাশি শুনিয়ে-মনোবিকারের চিকিৎসা করার চেষ্টা করতেন : এই চেষ্টা থেকেই হয়তো পিথাগোর-পন্থীদের মাথায় আসে। সংগীতের আত্মাকে পরিশোধিত করার কল্পনা। এবং একথায় কোনো সন্দেহই নেই যে, প্লেটোর “রিপাবলিক”-এর প্রথমাংশে আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবার সময় সংগীতের উপর অতখানি বোক দেবার যে-চেষ্টা, তার মূলে রয়েছে পিথাগোর-পন্থীদের প্রেরণাই।
আত্মার জন্যে চাই সংগীত, যেমন দেহের জন্যে ব্যায়াম-প্লেটোর গ্রন্থে (“রিপাবলিক”)। সক্রেটিস বলেছেন অত্যন্ত জোর গলায়! শুধু তাই নয়। প্লেটোর অপর গ্রন্থে (“ফিডো”) সক্রেটিস বলেছেন, “দর্শন হলো চূড়ান্ত সংগীত”। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা সুনিশ্চিতভাবে বলতে চান, এ-উক্তি আসলে পিথাগোর-পন্থীদের উক্তিই। অর্থাৎ, প্লেটোর রচনায় পিথাগোরীয় চিন্তাধারার নানামুখী প্রভাবের মধ্যে এও একটা প্ৰভাব। এবং সংগীতের মূল্যাটা . পিথাগোর-পন্থীদের কাছে অমন বিরাট বলেই য়ুরোপীয় ইতিহাসে ওরাই প্ৰথম সংগীত-বিজ্ঞান রচনায়মান দেন। সংগীত সম্বন্ধের্তারা যে মতবাদ দাঁড় করিয়েছিলেন, তাঁর মূল্য নিশ্চয়ই কম নয়। কিন্তু সে-মূল্য যতখানির হোক না কেন, কর্মজীবনের হাতিয়ারের বদলে নিছক সংগীতের কাছ থেকে দার্শনিক চিন্তাধারার কাঠামো সংগ্ৰহ করবার চেষ্টাকে প্ৰতিক্রিয়ার চিহ্ন বলেই স্বীকার করতে হবে। কেননা, মনে রাখতে হবে, আদিম সাম্যজীবন শেষ হবার পর থেকেই সংগীতের সঙ্গে মুছে গিয়েছে সমবেত আবেগ-উদ্দীপনার সম্পর্ক। সংগীত-বিশেষ করে গ্ৰীক সমাজের সদর মহলে যে যন্ত্রসংগীতের সমাদর সেই সংগীত (কেননা গণ-সংগীতের কথাটা আলাদা, সমাজের নিচু স্তরটায় গণ-সংগীতের সঙ্গে আজো মেহনত-জীবনের সম্পর্ক)-পরিণত হয়েছে বিলাসী শ্রেণীর অবসর-বিনোদনে। তাই, সংগীতের কাছ থেকে দার্শনিক চিন্তাধারার কাঠামো জোগাড় করবার চেষ্টাটা মেহনত-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পরিচয়ই।
প্ৰবাদ আছে, পিথাগোরাস একবার এক কামারশালের পাশ দিয়ে -চলেছিলেন। কামারশালে হাতুড়ি পেটার শব্দ : নানান কামার নানান ওজনের হাতুড়ি পিটছে, তাই শব্দও নানান রকমের,–যেন যন্ত্রের নানান পর্দায় নানান স্বর।। থমকে দাড়ালেন পিথাগোরাস, ভাবলেন, কপালে যে এমন সুযোগ জুটে গেল তা করুণাময়ের অশেষ করুণা ছাড়া আর কী? কিন্তু সুযোগটা ঠিক কীসের? ওই নানান ওজনের হাতুড়িতে যে নানান পর্দার সুর, তাই নিয়ে পরীক্ষা করবার সুযোগ। বীণা বাজাবার সময় বিভিন্ন তারে যে বিভিন্ন পর্দার সুর, তাও কি তাহলে তারগুলোর ওজনের ওপর নির্ভর করে? এই নিয়ে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করলেন পিথাগোরাস। প্ৰবাদটা সত্যি না মিথ্যে, তা নিয়ে আলোচনা তুলে লাভ নেই। কিন্তু এই প্রবাদটার মধ্যে পিথাগোর-পন্থীদের মেজাজটা খুঁজে পাওয়া যায়। কামারশালের পাশ দিয়ে চলেছেন দার্শনিক, কিন্তু নজরটা মেহনতের উপর নয়, কামারদের উপর নয়। এর মধ্যে যতটুকু শৌখিনতার দিক, বিলাসের দিক-শব্দের ওই ঠুং-ঠাং-টুকু –দার্শনিকের নজর শুধু তারই উপর। আইওনীয় দার্শনিকদের বেলায় মেহমন্তজীবন থেকে, মেহনতের হাতিরার থেকে-দার্শনিক চিন্তাধারার মূল কাঠামো সংগ্ৰহ করবার চেষ্টা। তাই সুস্থ বস্তুবাদের দিকে ঝোঁক; পিথাগোর-পন্থীদের মতো। রহস্যবাদ। আর অধ্যাত্মবাদের দিকে ঝোক নয়। কিন্তু বিজ্ঞান? গণিতশাস্ত্র?-এইখানে পূর্বপক্ষ একটা দারুণ আপত্তি তুলবেন। পিথাগোরপন্থীদের দার্শনিক প্ৰচেষ্টায় পিছনে গণিতশাস্ত্রের যে বিরাট প্রভাব, তাকে তো উড়িয়ে দেওয়া চলে না। পিথাগোরাস নিজে গণিতশাস্ত্রে একজন দিকপাল পণ্ডিত ছিলেন, জ্যামিতিতে তার অবদান আজও আমাদের পাঠ্যপুস্তকে পড়তে হয় (“পিথাগোরাসের থিয়োরেম”)। শুধু তাই নয়। “সংখ্যা”-কে পরম সত্য মনে করাটা থেকেই বুঝতে হবে, গণিতবিজ্ঞানের প্রেরণাই পিথাগোর পন্থীদের দার্শনিক প্রেরণার মূল উৎস। গণিতবিজ্ঞানকে তো বিজ্ঞানের মৰ্যাদা দিতেই হবে। তাই এই বৈজ্ঞানিক প্রেরণাকে উপেক্ষা না করে পিথাগোর-পন্থীদের দর্শনে শুধুমাত্র প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন খোঁজা সম্ভব নয়।
উত্তরে বলব, গণিত-বিজ্ঞানকে তুচ্ছ করবার তাগিদটা নিশ্চয়ই ভ্ৰান্ত। কিন্তু সেইসঙ্গে এ-কথাও মনে রাখা একান্ত দরকার যে, যুগে যুগে গণিতবিজ্ঞান দর্শনশাস্ত্রের পক্ষে এক মরীচিকার সৃষ্টি করেছে। এ-কথা কাণ্ট প্রমাণ করেছেন অত্যন্ত স্পষ্টভাবে। কথাটাকে ভালো করে না বুঝলে পিথাগোর-পন্থীদের দর্শনকে ঠিকমতে যাচাই করা যাবে না।
আসলে, গণিত-বিজ্ঞানের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করবার ব্যাপারে একটা মস্ত।বড় ফাকির সম্ভাবনা। কেননা, আপাত-দৃষ্টিতে মনে হতে পারে, এ-বিজ্ঞান যা নিয়ে আলোচনা করে তা বাস্তবজগতের বা মূর্তজগতের ধরাছোয়ার বাইরে, মনে হতে পারে অতীন্দ্ৰিয় বিশুদ্ধ চেতনা-গ্ৰাহ সংকেতময় সত্তাই গণিতশাস্ত্রের প্ৰকৃত আলোচ্য। যেমন ধরুন, পাটীগণিতের সংখ্যা বা জ্যামিতির গড়নগুলো। পাটীগণিত বলছে, ৫ + ৭ = ১২। কিন্তু ৫ বলে কিছু, ৭ বলে কিছু, কিংবা ১২ বলে কিছু মূর্ত জগতের কোথাও নেই; মূর্ত জগতে আছে এটা গোরু, ৫টা ভেড়া কিংবা ওই ধরনের নানান রকম জিনিস। গোরু আছে, ভেড়া আছে বাস্তব পৃথিবীতে; কিন্তু বিশুদ্ধ ৫ বা বিশুদ্ধ ৭ নেই কোথাও। অথচ পাটীগণিতের আলোচনাটা তো গোরু ভেড়া নিয়ে আলোচনা নয়; আসল আলোচনা হলো ওই বিশুদ্ধ সংখ্যাগুলি নিয়ে। এই সংখ্যাগুলির কথা আমরা বড় জোর ভাবতে পারি, এগুলি নিয়ে চিন্তা করতে পারি; কিন্তু বাস্তব জগতের কোথাও এগুলির সন্ধান ‘মেলে না। কিংবা ধরা যাক জ্যামিতিতে আলোচ্য বিষয়গুলি। বিন্দু কিংবা সরল রেখা কিংবা ত্রিভুজ। বিন্দুর শুধু অবস্থান আছে, কিন্তু দৈর্ঘ্য-প্ৰস্থ বলে কিছু নেই। এমনতর জিনিস নিয়ে মাথা ঘামানো যায়, কিন্তু এমনতর জিনিস বাস্তব দুনিয়ার কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। কিংবা ধরা যাক, সরল রেখা। তার শুধু দৈর্ঘ্য আছে, কিন্তু প্ৰন্থ বলে কিছু নেই। অথচ, বাস্তব পৃথিবীতে যত সূক্ষ্ম রেখাই আপনি আঁকুন না কেন, তার কিছু না কিছু প্ৰস্থ তো থাকতে বাধ্য। প্ৰস্থ বাদ দিয়ে শুধু দৈর্ঘ-সম্পন্ন জিনিসের কথা কল্পনা করা যায়, কিন্তু পৃথিবীর কোথাও তার চিহ্ন পাওয়া অসম্ভব। তাই জন্যেই তো জ্যামিতিতে বলে : “ধরা যাক ABC হলো একটা ত্রিভুজ”, কিংবা “ধরা যাক AB একটা সরল রেখা”। তার মানে, কাগজের ওপর আমরা যে সরল রেখাটা কিংবা যে ত্রিভুজটা আঁকছি, আসলে সেটা সরল রেখা নয় কিংবা ত্রিভুজ নয়। তাই, “ধরা যাক” বলে বলি। যেমন, একটা পেনসিল দেখিয়ে যদি বলা যায়, “ধরা যাক এটা একটা টেস্ট-টিউব”। তার মানে, পেনসিলটা টেস্ট-টিউব নয়, তবু আপাতত কাজ চালাবার আশায় ওটাকেই টেস্ট-টিউব বলে কল্পনা করবার চেষ্টা। তবু টেস্ট-টিউব বাস্তব দুনিয়ায় খুঁজে পাওয়া যায়, পাওয়া যায় না জ্যামিতির বিষয়গুলি, সেগুলি তাই একান্তভাবে বুদ্ধিগ্রাহ, বাস্তব দুনিয়ার কোনো কিছু নয়।
গণিতের স্বরূপ উপলব্ধি করতে গেলে আপাতত এই রকমের একটা কথাই মনে হতে পারে, মনে হতে পারে-এ-বিজ্ঞানের আলোচ্য যে-বিষয় নিয়ে, তা বাস্তব জগতের জিনিস মোটেই নয়, বিশুদ্ধ চিন্তাজগতের জিনিস। আর তাই, দর্শন যদি গণিতশাস্ত্রের কাছ থেকে প্রেরণা পেতে চায় তাহলে দর্শনও বিশুদ্ধ চিন্ময়ের সন্ধান ছাড়া আর কী হতে পারে? আসলে কিন্তু এই মনেহওয়াটা একেবারে ভুল মনো-হওয়া। কেননা, কাণ্ট যেরকম দেখিয়েছিলেন, গণিত নিয়ে আলোচনা করতে গেলে মূর্ত জগতের অভিজ্ঞতার দ্বারস্থ না হয়ে উপায়ই নেই। কাণ্ট বলেছেন, ৫ আর ৭ যোগ দিলে যে ১২ হয়, এ-কথা শুধুমাত্র মাথা-ঘামিয়ে জানতে পারা সম্ভবই নয়। ৫-এর ধারণা আর ৭-এর ধারণা আর যোগ-চিহ্নের ধারণা-এ-সব নিয়ে আপনি যতই মাথা ঘামান না কেন, এই ধারণাগুলিকে যে-ভাবেই বিশ্লেষণ করুন না কেন, এর মধ্যে ১২-র ধারণা আবিষ্কার করা একেবারেই অসম্ভব। ১২-র ধারণা পেতে গেলে মূর্ত অভিজ্ঞতার দ্বারস্থ না হয়ে উপায় নেই; হয়তো পাঁচটা ঘুটি আর সাতটা ঘুটির যে মূর্ত অভিজ্ঞতা তার দ্বারস্থ হতে হবে। কিন্তু যেভাবেই হােক না। কেন, অভিজ্ঞতার নির্ভর একেবারে বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ বুদ্ধির দৌলতে কখনোই জানা যায় না ৫+৭=১২। জ্যামিতির বেলাতেও তাই; জ্যামিতির গড়নগুলি নিয়ে আলোচনা করবার সময়ও মুর্ত অভিজ্ঞতার দ্বারস্থ না হয়ে কোনো উপায় নেই। তাই আঁকজোঁক করতে হয়, ছবি আঁকতে হয়।
এই হলো কাণ্টের সমালোচনা। অবশ্যই, কাণ্টের সমালোচনায় প্রধান বোকাটা হলো ইন্দ্ৰিয়-অভিজ্ঞতার দিকে; গণিত-বিজ্ঞান বিশুদ্ধ চেতনার বা শুধুমাত্ৰ বুদ্ধির উপর, মাথা ঘামানোর উপর নির্ভর করে না; তা একান্তভাবেই নির্ভর করতে বাধ্য ইন্দ্ৰিয়-অভিজ্ঞতার উপরও। কিন্তু এ সমালোচনার উপর নিভর করে আর এক-পা এগিয়ে গেলেই বুঝতে পারা যাবে, গণিতবিজ্ঞান কেন একান্তভাবেই মূর্ত আর বাস্তব পৃথিবীর মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য। আসলে, ইন্দ্ৰিয়-অভিজ্ঞতা শূন্য থেকে স্বাক্ট হয় না; তার অনিবাৰ্য উৎস হলো বস্তু-জগৎ, মূর্ত পৃথিবী। তাই অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করা মানেই মূর্ত বস্তুজগতের উপর নির্ভর করা। তাছাড়া, গণিত-বিজ্ঞানের জন্ম-ইতিহাসের কথাটাও মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, বাস্তব পৃথিবীর সঙ্গে সংগ্রামের মধ্যেই এ-বিজ্ঞানের জন্ম। তাই মূর্ত্য-জগতের সঙ্গে, বস্তুজগতের সঙ্গে এ-বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠতা নানান দিক থেকে।
অথচ, আপাতদৃষ্টিতে তা মনে হয় না। খেয়াল থাকে না, গণিতবিজ্ঞান বাস্তব জগতের সঙ্গে কী ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ। মনে হয়, বিশুদ্ধ চিন্ময় নিয়েই বুঝি তার আলোচনা। আর তাই, গণিতের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে দর্শন রচনা করবার সময় দেখতে পাওয়া যায়, দার্শনিকেরা যুগে যুগে এক চরম ভ্ৰান্তির মধ্যে গিয়ে পড়েছেন। তঁরা মনে করছেন, গণিতবিজ্ঞানে যেহেতু বিশুদ্ধ চিন্ময় বিষয় নিয়ে আলোচনা এবং যেহেতু দর্শনকেও ঢালতে হবে। গণিতবিজ্ঞানের ছাচে, সেইহেতু দর্শনের বেলাতেও মূর্ত জগতটা সম্বন্ধে, বাস্তব দুনিয়া সম্বন্ধে হুশি থাকবার কথা নয়। এই জন্যেই কাণ্ট বলেছেন, গণিতবিজ্ঞান অনেক সময় দর্শনকে পথ ভুলিয়েছে, মায়া-মরীচিকা যেরকম পথ ভুলোয় পথিককে।
এ-কথায় কোনো সন্দেহ নেই যে, পিথাগোর-পন্থীদের বেলায় এইরকম একটা মন্তব্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্ৰযোজ্য। গণিতবিজ্ঞানের কাছ থেকে তাঁরা প্রেরণা পেয়েছেন, কিন্তু প্রেরণাটা বৈজ্ঞানিক প্রেরণা নয়। তাই। এই তথাকথিত প্রেরণা তাদের বিজ্ঞানের পথ থেকে সরিয়ে বিজানবিরোধী অধ্যাত্মবাদের পথে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে। এ-কথার আরো স্পষ্ট প্রমাণ হলো বিজ্ঞানের আদর্শ নিয়ে তঁদের মতবাদ। প্ৰকৃতির সঙ্গে, বাস্তব দুনিয়ার সঙ্গে সংগ্রামের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো বিজ্ঞান; কিন্তু পিথাগোর-পন্থীদের চেতনা থেকে সে-কথা মুছে গিয়েছিল। তাদের কাছে বিজ্ঞানের একমাত্র আদর্শ হলো আত্মাকে শুদ্ধ করবার আদর্শ। সংগীতের মতো গণিতবিজ্ঞানও চিত্তশুদ্ধির উপায় মাত্র। এমন-কী, তলিয়ে দেখতে গেলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্ধেশ্বটাও তাই। কেননা, পিথাগোর-পন্থীদের কাছে যদিও আপাতত মনে হয় চিকিৎসা বিজ্ঞান দেহকে নীরোগ করবার উপায়, তবুও দেহকে নীরোগ করবার সবচেয়ে বড় তাগিদ হলো আত্মার জন্যে উপযুক্ত আর পরিচ্ছন্ন বাসস্থান নির্ণয় করা।
সমস্ত কিছু উদ্দেশ্যর কেন্দ্ৰ তাই আত্মা।
আত্মা নিয়ে এমনতর মাথা ঘামানো আইয়োনীয় দার্শনিকদের বেলায় মোটেই নয়। বহির্জগতের সঙ্গে মানুষের যে সংগ্রাম, অর্থাৎ মেহনত, সেই সংগ্রামে অংশীদার ছিলেন আইওনীয় দার্শনিকেরা। ফলে, তাদের সমস্যাটা বহির্জগৎকে নিয়েই। বস্তুজগতের প্রকৃত রূপ বুঝতে চেয়েছিলেন তারা। কিন্তু পিথাগোর-পন্থীদের সমস্ত উদ্দেশ্যটাই অন্তমুখী। তার কারণ, মেহনতের সঙ্গে সম্পর্ক গেছে ঘুচে, তাই সমস্যাটা বাইরের জগৎ নিয়ে নয়, মনের জগৎ নিয়ে। অর্থাৎ আত্মা নিয়ে। তার মানেই কিন্তু বিজ্ঞান ছেড়ে ধর্মের আশ্রয়ে এসে পড়ার চেষ্টা। কেননা, ধর্মের যেটা সবচেয়ে মূল কথা, সে-কথা হলো বাইরের জগৎকে বদলাবার বদলে মানস জগৎকে বদল করবার কথা।
ধর্মমোহকে পিছনে ফেলে এগিয়ে আসতে পেরেছিল বলেই আইওনীয় দর্শনের অতখানি গৌরব। সেই ধর্মমোহের কাছে ফিরে যেতে চাইল পিথাগোরাসের দর্শন। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা তর্ক করেন, ঠিক কোন দেশের ধর্মবিশ্বাস পিথাগোর-পন্থীদের দর্শনে প্রভাব বিস্তার করছিল তাই নিয়ে। কেউ বলেন, ধর্মবিশ্বাসটার আমদানি হলো মিশর থেকে, কেউ বলেন। ভারতবর্ষ থেকে, আবার কেউ বা বলেন তা নয়, এ-ধর্ম-বিশ্বাস গ্ৰীক জমিতেই জন্মেছে, হোমার-এর চেয়ে প্রাচীন কবি আফিউস এ-ধর্মের আদিম প্ৰতিষ্ঠাতা, তাই এর নাম অফিক-ধর্মবিশ্বাস। অবশ্যই, ঠিক কোথা থেকে যে এই ধর্মবিশ্বাসের আমদানি হলো সেটা মোটেই বড় প্রশ্ন নয়। বড় কথা হলো, দর্শনের আঙিনায় এল ধর্মবিশ্বাস; বড় কথা হলো এই প্ৰতিক্রিয়ার কথাটাই।
পিথাগোর-পন্থীদের দর্শনে জন্মান্তরবাদ; এ দেহটা অমর আত্মার একটা অস্থায়ী ডেরা-মাত্র। আত্মা দুদিন পরেই এ-ডেরা ছেড়ে যাবে, আশ্রয় নেবে অন্য দেহে, অন্য ডেরায়।
পিথাগোর-পন্থীদের দর্শনে পাপ-পুণ্য নিয়ে পুরোদমে আলোচনা। পাপের সম্ভাবনা থেকে মুক্তি পাবার আশায় এবং অর্জিত পাপ স্বালন করবার আশায় হরেকরকম বিধি-নিষেধের বর্ণনা।
পিথাগোর-পন্থীরা মনে করতেন, মানুদের দল ভেড়ার পালের মতো; এই পালের চরম মালিক হলেন ভগবান। তাই মানুষের উদ্দেশ্য হলো, জীবনকে পবিত্র করে তোলা, যাতে সেই মালিকের মনস্তুষ্টি হয়।
–এই সব কথাই শেষ পর্যন্ত পিথাগোরপন্থীদের দর্শনের মূল কথা। অথচ এগুলি সবই ধর্মমোহের সনাতন অঙ্গমাত্র।
তাই পিথাগোর-পন্থীদের সময় থেকেই ইওরোপীয় দর্শনের আঙিনায় ধর্মের নিশান উড়ল।
গ্ৰীক দর্শনের আদি যুগটার কথা কিন্তু অন্যরকম।
প্ৰাচীন ভারতীয় দর্শনের আদি যুগেও বস্তুবাদের কথা, আর সেই বস্তুবাদের তীব্র সংগ্ৰাম ধর্মের বিরুদ্ধে।
০৮. অকৰ্মণ্য পুরোহিতশ্রেণী
“না আছে বুদ্ধি, না খেটে খাবার মত গতর; এমনতর অকৰ্মণ্য যে পুরোহিতশ্রেণী, তাদেরই একটা হিল্লে হিসেবে রচিত হয়েছে অগ্নিহোত্র যজ্ঞের কথা, তিন তিনটে বেদ, এবং এইরকম আরও অনেক কিছু। আসলে স্বৰ্গ, অপবর্গ বা পারলৌকিক আত্মা বলে সত্যি কিছু নেই।”
ভাবতে অবাক লাগে : অন্তত আড়াই হাজার বছর আগে আমাদের দেশে এই রকম সাংঘাতিক কথা শুনতে পাওয়া গিয়েছিল। শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে আক্ৰোশটা স্পষ্ট। তবু শুধু আক্ৰোশ নয়, সহজ বুদ্ধির নির্মল খণ্ডনপদ্ধতিও। চাৰ্বাকপন্থী যেমম বলেন। কর্মজীবনের কষ্টিপাথরে শাসক-শ্রেণীর দাবিগুলোকে ঘষে দেখো, দেখবে কী অসম্ভব রকমের মেকি।
“জ্যোতিষ্টম যজ্ঞে নিহত পশু যদি সোজা স্বৰ্গেই যায়, তাহলে যজমান কেন নিজের ব্যাপকে হাড়িকাঠে ফেলে না? শ্ৰাদ্ধাপিণ্ড যদি পরলোকগীত মানুষের পেট ভরাতে পারে, তাহলে কেউ বিদেশ যাবার সময় তার সঙ্গে চিড়েমুড়ি বেঁধে দেবার আর দরকার কী? (ঘরে বসে তার উদ্দেশে পিণ্ডি দিলেই তো চলা উচিত; হাজার হোক পরলোকের চেয়ে ইহলোকেরই দেশান্তর অনেক কাছে-পিঠের ব্যাপার)। কিংবা, স্বৰ্গে বসে পৃথিবীতে দেওয়া পিণ্ডে যদি কারুর সাধ মেটে, তাহলে ছাদে বসে মাটিতে দেওয়া পিণ্ডে তার পেট ভরে না কেন?’
এই যেন চাৰ্বাকপন্থীর খাঁটি দার্শনিক পদ্ধতি। কূট তর্কের দিকে ঝোঁক কম, মৌলিক চাৰ্বাক্যবাদে একান্তই তা ছিল কিনা ভেবে দেখবার কথা। কাজের ক্ষেত্রে, আটপৌরে দৈনন্দিন জীবনে যাচিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে কোন দর্শনের কতখানি দৌড়। অবশ্য এমন খোলাখুলি এই পদ্ধতির কথা তাঁরা বলতেন কি না জানা নেই; খুব সম্ভব বলতেন না,–দর্শনের পদ্ধতি নিয়ে তখনকার দিনে আজকালকার মতো এত তর্কাতকি নিশ্চয়ই ছিল না। তা ছাড়া চার্বীক-দৰ্শনের কোনো সম্পূর্ণ পুঁথি আমাদের কাছ পর্যন্ত তো এসে পৌঁছয়নি, যদিও যে-সব খণ্ড বিক্ষিপ্ত শ্লোক আজো টিকে রয়েছে তার থেকে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, কোনো-না-কোনো সময়ে এ দর্শনের উপর সম্পূর্ণ গ্ৰন্থ নিশ্চয়ই রচিত হয়েছিল। সে পুঁথি বিলুপ্ত হয়েছে। এ ঘটনাকে শুধুই শতাব্দীর শোভাযাত্রার ফল বলে বর্ণনা করা চলবে না, কেননা শতাব্দীর শোভাযাত্রা সত্ত্বেও তো প্ৰাচীনতর অন্যান্ত গ্ৰন্থ বিলুপ্ত হয়নি। বরং অনুমান করা স্বাভাবিক যে, বিজয়ী ব্ৰাহ্মণ্য শ্রেণী দেশের বুক থেকে এই সাংঘাতিক নাস্তিক্যবাদের সমস্ত কীর্তিকলাপ ধুয়েমুছে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল। এই প্ৰচেষ্টার বহুমুখী স্বাক্ষর আছে। তবু এই দর্শনের যে সমস্ত টুকরো বিক্ষিপ্ত চিহ্ন আজও বর্তমান, তা থেকে এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, চার্বাকদের ব্ৰাহ্মণ্যবিদ্বেষ নিছক বিদ্বেষ ছিল না, রীতিমত দার্শনিক ভিত্তির উপর তার প্রতিষ্ঠা ছিল এবং বিপক্ষের বহুমুখী প্ৰচেষ্টা সত্ত্বেও এ মতবাদকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দেওয়া কোনোদিন সম্ভব হয়নি। একথার সপক্ষে বহু প্রমাণের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হলো মাধবাচার্যের “সর্বদর্শনসংগ্ৰহ”। প্ৰায় ছশো বছর আগে লেখা এই পুঁথি, দেশের দার্শনিক আলোচনার আসর তখনো রীতিমতো সরগরম। সংস্কৃতে লেখা ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের মধ্যে এ গ্ৰন্থ অন্যতম। তাই একে প্ৰামাণিক বলে না মেনে উপায় নেই। অন্যান্য আস্তিক লেখকদের মতো মাধবাচাৰ্য ঈশ্বর-বন্দনা করে গ্ৰন্থ শুরু করতে চেয়েছেন। কিন্তু এভাবে শুরু করতে গিয়েই তাঁর হুঁশ হয়েছে চাৰ্যাকদের কথা : তারা ঈশ্বর, আত্মা, পরলোক সবাই উড়িয়ে দিতে চায়। তাই, চাৰ্যাকবাদ খণ্ডন করে না নিলে ঈশ্বরস্তুতির ভিত মজবুত হয় না। এই সূত্রে মাধবাচাৰ্য একটি পরিপূর্ণ দার্শনিক মতবাদের বর্ণনা করেছেন, এমন-কী কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন, যা নাকি খোদ চাৰ্যাকপন্থীদের রচনা বলেই সাধারণত স্বীকৃত। সাধারণত এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনাটুকুকেই চাৰ্যাক দর্শনের প্ৰধান সম্বল বলা হয়। এ ছাড়া অবশ্যই চাৰ্যাক-দর্শনের খুচরো কথাবার্তা বিভিন্ন দার্শনিকদের গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া যায়, কিন্তু সমস্তটাই পূর্বপক্ষ হিসেবে। এ সব থেকে অন্তত একথা নিশ্চয়ই প্ৰমাণ হয় যে, এ দর্শন সম্বন্ধে কোনো কালে কোনো সম্পূর্ণ গ্ৰন্থ লেখা হোক আর নাই হোক এবং সে-সব পুঁথি দেশের বুক থেকে বিলুপ্ত করারার জন্যে বিপক্ষ দলের চেষ্টা থাকুক। আর নাই থাকুক,- মতবাদটা দেশের দার্শনিক সমাজে এককালে রীতিমত শোরগোল সৃষ্টি করেছিল। নইলে একে খণ্ডন করবার জন্যে সমস্ত দার্শনিক দিকপালের এত মাথাব্যথাই বা হবে কেন? মাধবাচাৰ্য তো সোজাসুজি মেনে নিয়েছেন : দুরুচ্ছেদং হি চাৰ্বাকস্য চেষ্টতম্, চাৰ্বাক মত উচ্ছেদ করা নেহাত চাট্টিখানি কথা নয়।
তবু এ মত উচ্ছেদ করবার জন্যে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। তাই এই দর্শনের যিনি প্ৰতিষ্ঠাতা বা প্ৰধান প্রচারক, তার নামটুকু পর্যন্ত ইতিহাস থেকে বেমালুম মুছে দেওয়া হয়েছে। কোনো কোনো আধুনিক পণ্ডিত অবশ্য সোজাসুজি মনে করেন যে, চাৰ্বাক বলেই এক ব্যক্তি এ দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, তার নাম অনুসারেই দর্শনটার নামকরণ। কিন্তু দেশের প্রবাদ ও ঐতিহে। এ মতের কোনো সমর্থন নেই। বরং প্ৰবাদ আছে যে, দেবতাদের গুরুদেব বৃহস্পতি এককালে কোনো এক কৃটি অভিপ্ৰায় চরিতাৰ্থ করবার উদ্দেশ্যে এই মতবাদের প্রবর্তন ও প্রচার করেছিলেন। মাধবাচাৰ্যও চাৰ্যাকদের সোজাসুজি “বৃহস্পতিমতানুসারী” বলেই বর্ণনা করেন। এই প্ৰবাদ, এবং এর মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যের বিকৃত তথ্য আছে, তার আলোচনা পরে করব। আপাতত প্ৰশ্ন উঠবে; যদি তাই হয়, তাহলে “চার্বাক’ নাম এল কোথা থেকে? আধুনিক পণ্ডিতেরা শব্দার্থের বিচারে এ প্রশ্নের জবাব খোঁজেন। হতে পারে, সাধারণ লোকের মন্নভোলানো কথা বলত বলে–চারু +বাক্-এদের নাম চাৰ্বাক। হতে পারে চর্ব শব্দ থেকে এ নামের উৎপত্তি, অর্থাৎ চাৰ্বাক হলো সেই দার্শনিকের নাম, খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে যে খুঁজত পরম পুরুষাৰ্থ।
চাৰ্যাকপন্থী যে সাধারণ মানুষের মনে ধরবার মত কথা বলুতেন, এ বিষয়ে অবশ্য সন্দেহের অবকাশ নেই। কেননা জনগণের সহজ কর্মবোধের কাছে এই লোকায়ত জগৎই একমাত্র সত্য। কৃষক জানে, তার পায়ের তলায় মাটি আর মাথার উপরে মেঘ-পৃথিবীর সমস্ত দার্শনিক তত্ত্বের চেয়ে ঢের বেশি সত্য। এই মাটিতে লাঙল দিয়ে সে যে সোনার ফসল ফলায়, তা মায়া নয়, মনের খেয়ালী ধারণা নয়, আর এই সোনার ফসলের প্রায় সবটুকু যখন ওঠে জোতদারের গোলায়, তখন কৃষকের পেটে যে বাস্তব জ্বালা ধরে তার উপর অনেক রকম আধ্যাত্মিক প্ৰলেপ মাখিয়ে তবে ঠাণ্ডা রাখতে হয়। পেটটা হলো মনের ধারণা, আর খালি পেটের যন্ত্রণাটা দীর্ঘ স্বপ্নের মতো প্ৰতিভাসিক-এমনতর। কথা শুধু তারই স্বার্থে রঞ্জিত, যে নিজে চাল উৎপাদন করতে নারাজ অথচ নৈবেদ্যর চাল দিয়ে সংসার চালাতে নিপুণ। ধুলোমাটির গ্লানিমুক্ত এক চিন্ময় জগতের কথা জনগণের দর্শন হতে পারে না, জনগণের মনে ধরবার মতো কথাই চাৰ্বাক দর্শনের কথা। আর জনগণের দর্শন বলেই খিদে পেলে পেট ভরে খাবার কথা বলতে এ দর্শনের চক্ষুলজা নেই। চর্বণ ব্যাপারটা সাধারণ মানুষের কাছে অগৌরবের কিছু নয়,–আভিজাতিক সমাজের ক্ষীণাঙ্গির কাছে চর্বণ জিনিসটা যত হীন আর নীচ পশুবৃত্তির পরিচয়ই হোক না কেন। তাই, একথা যদি প্রমাণও হয় যে, চর্ব শব্দ থেকে তাদের দর্শনের নামকরণ হয়েছে, তাহলেও জনগণের পক্ষে কান লাল করবার কোনো কারণ নেই, সম্ভাবনাও নেই।
শ্ৰেণী-সংগ্রামের আলোচনায় এসে পড়তে হয়। একদিকে জনগণ আর তাদের লোকায়ত দর্শন, অপরদিকে পুরোহিত শ্রেণী, যাগযজ্ঞ। আর পারলৌকিক আত্মার কথা। একদিকে নিদেন পেট ভরে খাবার কথা, (যদিও ধার-করে ঘি খাওয়ার উৎসাহটা নিশ্চয়ই অপপ্রচারের দরুন)। অপর দিকে ইহজীবনে উপবাসী থেকে পুরোহিত ভোজন করিয়ে পরলোকে পরমান্ন পাবার স্বচ্ছ যুক্তি। প্রাচীন ভারতীয় দর্শনেও শ্রেণী সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি! একে অত্যাধুনিক ছাত্রের উদ্ধত কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মাধবাচার্যের বইতে খোদ চাৰ্বাকপন্থীর যে শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে, তার মধ্যেও শ্রেণী-সংগ্রামের ইঙ্গিতটুকু স্পষ্ট :
“মৃতের উদ্দেশে প্ৰেতকাৰ্য প্রভৃতি ব্ৰাহ্মণদের জীবনোপায় ছাড়া আর কিছু নয়। যারা তিন তিনটে বেদ রচনা করেছে তারা বেবাক ভণ্ড-ধূর্ত-নিশাচরের দল।”
“ভণ্ড-ধূর্ত-নিশাচরাঃ” : শুনতে যে রুচিতে বাধে, মনে হয়। কাঁচা খিস্তি। দর্শনের ‘নৈর্ব্যক্তিক’ আলোচনায় এ রকম শালীনতার অভাব কেন? কিন্তু মুশকিল এই যে, “ছোটলোকের” দল শাসকের বিরুদ্ধে যখন রুখে দাঁড়ায়, তখন তাদের কাছে সুরুচি, শালীনতা প্ৰভৃতি তথাকথিত ‘মনুষ্যধর্মগুলো লোকঠকানে সাধুবাক্যেরই অঙ্গবিশেষ মনে হতে পারে বই কী! বিপক্ষের সাধুপুরুষমাত্রই জানেন যে, বিপ্লবের সময় রক্তাক্ত বীভৎসতা করতে পর্যন্ত ‘ছোটলোক’দের রুচিতে বাধে না, খিস্তি খেউড় তো নেহাত ছোট ব্যাপার। তবু সমাজে শ্ৰেণীসংগ্রাম এক জিনিস-এবং দার্শনিক দ্বন্দ্ব তার প্রতিবিম্ব হলেও হাজার হোক স্বতন্ত্র স্তরের ব্যাপার। বাষ্প জল ছাড়া কিছুই নয়, তবু শুধু জলও নয়–শুধু জলে এঞ্জিন চলে না, বাম্পে চলে; তাই বাম্পের আইনকানুনও আলাদা। মানুষের দার্শনিক চেতনা জিনিসটিরও সেই অবস্থা। বাস্তব সমাজের ঘাতপ্ৰতিঘাতেই তার জন্ম, তবু নিছক এই ঘাতপ্ৰতিঘাত দিয়ে তার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয় না। তার আইনকানুন আলাদা। তাই কোনো দার্শনিক মতবাদ প্ৰতিষ্ঠা করতে হলে শুধু শ্রেণী:স্বার্থের উল্লেখ করলেই চলবে না। মাটির পৃথিবীতে মজবুত খুটি ছিল বলেই আমাদের দেশের চার্বাকপন্থীরাও সুস্থ জড়বাদের এই প্ৰাথমিক সত্যকে যেন অস্পষ্টভাবে অনুভব করতেঁ পেরেছিলেন। বিপক্ষদলের শ্ৰেণীস্বার্থের দিকটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেই চলবে না। কেননা, বিপক্ষের হাতে আছে দার্শনিক পদ্ধতির এক অপূর্ব সুদৰ্শনচক্র, সে অস্ত্ৰ দিয়ে সমস্ত জড়বাদ তারা অবলীলায় খণ্ড খণ্ড করে ফেলতে পারে। এ অস্ত্ৰ হলো বিশুদ্ধ বিচার-বুদ্ধি, অভ্রান্ত তর্কপদ্ধতি। পরমসত্তা বিশুদ্ধ তর্কপ্ৰণালীর দাবি মানতে বাধ্য, বিপক্ষের কাছে। এ কথা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ এবং বুদ্ধির দাবি জড়বাদ কোনোমতেই মেটাতে পারে না। কিন্তু জড়বাদের প্রথম কথা হলো; বাস্তবজগৎ বুদ্ধির দাবি মানতে বাধ্য নয়, বরং বুদ্ধিই বাস্তব জগতের দাবি মানতে বাধ্য।
চাৰ্বাকপন্থীও বিপক্ষের শ্রেণীস্বার্থটুকু প্ৰকাশ করে দিয়ে ক্ষান্ত হননি, বিপক্ষকে নিরস্ত্র করতে কোমর বেঁধে লেগেছেন। বিশুদ্ধ তর্বাপদ্ধতি বলে, ব্যাপারটায় গোড়াতেই গলদ, তর্কের কোন দার্শনিক প্রতিষ্ঠা নেই। চাৰ্বাকপন্থী বলেন, তর্ক-পদ্ধতির সবচেয়ে মামুলি উদাহরণটা নিলেই এ কথা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যাবে। পর্বতঃ বহ্নিমান ধূমাৎ। ধূম দেখে পর্বতে বহি অনুমান করা সম্ভব। তার কারণ আমাদের স্থির বিশ্বাস-যাত্র যাত্র ধূমঃ তন্ত্র অত্র বহ্নি, যেখানে যেখনে ধুয়ো সেখানে সেখানেই আগুন। কিন্তু কথা হলো, এ রকম বিশ্বাস পোষণ করবার অধিকার কোথা থেকে পাওয়া সম্ভব? নিজেদের অভিজ্ঞতা ছাড়া আর কোনো অজুহাত থাকতেই পারে না, অথচ নিছক অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে “সমস্ত’ ধূম সম্বন্ধে কথা বলা নিশ্চয়ই দুঃসাহস। আমাদের অভিজ্ঞতা অতি স্বল্প-ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের সমস্ত ধূম এ অভিজ্ঞতার আওতায় আসতে পারেই না। চাৰ্যাকদের কথাটা আমাদের দেশের দার্শনিক পরিভাষায় প্ৰকাশ করতে গেলে বলতে হবে : অনুমান নির্ভর করে ব্যাপ্তির উপর, ব্যাপ্তি হলো হেতু বা লিঙ্গ (middle term : আলোচ্য উদাহরণে ধূম) এবং পক্ষ (major term : আলোচ্য উদাহরণে ‘বহ্নি’), এদের মধ্যে সামান্য-সম্বন্ধ (universal relation : আলোচ্য উদাহরণে “যত্র যত্র ধূমঃ তন্ত্র তত্ৰ বহ্নি)। চাৰ্বাকপন্থী বলেন, এই ব্যাপ্তি জিনিসটে কোনোদিন প্ৰতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। মানুষ বড় জোর বলতে পায়ে-যে-যে জায়গায় আমি ধুয়ো দেখেছি সেই সেই জায়গাতেই দেখেছি আগুন। কিন্তু আমি আপনি ক-জায়গায় ধুয়োই বা দেখেছি? অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সমস্ত ধুয়ো কেউ কখনো দেখেনি, দেখতে পারে না। কারুর পক্ষে তাই জোর গলায় বলবার অধিকার নেই; সমস্ত ধুয়োর সঙ্গে আগুনের যোগাযোগ থাকতে বাধ্য।
দৈনিক জীবনে সবচেয়ে সরল অনুমানের বেলাতেই যদি দেখি তর্কপদ্ধতির গোড়ায় গলদ রয়েছে, তাহলে দার্শনিকদের কুটতর্ককে সত্য অন্বেষণের অভ্রান্ত উপায় বলে মানবার কোনো মানেই হয় না। এবং অনুমানই যদি আচল বলে প্ৰমাণিত হয়, তাহলে প্ৰত্যক্ষ ছাড়া জ্ঞানের অন্যান্য তথাকথিত উৎসগুলোর উপর নির্ভর করতে যাওয়া নেহাতই মূঢ়তা, কেননা এগুলি সবই অনুমান-নির্ভর অর্থাৎ উপমান, আপ্তবাক্য প্রভৃতি জানের তথাকথিত উৎসগুলো শেষ পর্যন্ত দেউলে, কেননা এদের আসল সম্পত্তি বলতে অনুমান এবং অনুমান নেহাতই অচল। তাই চাৰ্বাকপন্থী বলেন, নিছক প্রত্যক্ষ দিয়ে যতটুকু জানা যায় ততটুকুকে সত্যি বলে মানব। অবশ্য এ কথা ঠিক, চাৰ্যাকদের এই অনুমান-খণ্ডন বিচার-সহও নয়, বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের পক্ষে অনিবাৰ্যও নয়। বরং এর থেকে চরম ভাববাদ এবং সন্দেহবাদ এসে পড়াই স্বাভাবিক-যেমন এসেছিল ইংরেজ দার্শনিক হিউমের বেলায়। তবে এখানে একটা প্রশ্ন তোলা যায়; যদিও মাধবাচাৰ্য চাৰ্যােকদের এই ব্যাপ্তি-খণ্ডন পদ্ধতির নিখুঁত বৰ্ণনা করেছেন, তবুও চাৰ্বাকদর্শনে এমন খুঁটিয়ে অনুমান-পদ্ধতিকে খণ্ডন করবার চেষ্টা সত্যি কি ছিল? আমার বিশ্বাস তা ছিল না, থাকার কথা নয়। কেননা, মৌলিক চাৰ্বাকদর্শনের প্রচলন ও প্রভাব হয় অন্তত খ্ৰীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে। সে যুগে জ্ঞানের উৎস নিয়ে দেশে এমন কূটতর্কের রেওয়াজই থাকা সম্ভব নয়। তাই সে-যুগে এমন খুঁটিয়ে ব্যাপ্তি জিনিসটে কেউ যে খণ্ডন করতে চেয়েছিলেন, তা নেহাতই অসম্ভব বলে মনে হয়। তাহলে মাধবাচাৰ্য ব্যাপ্তি-খণ্ডনের এই নিখুঁত বর্ণনা দিতে গেলেন কেন? তার কারণ হয়তো মৌলিক চাৰ্বাকদর্শনে যদিও সমস্ত অনুমানকেই উড়িয়ে দেবার উৎসাহ ছিল না, তবুও নিশ্চয়ই সুস্থ বস্তুবাদীর বিশুদ্ধ-বুদ্ধি-বিদ্বেষটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ মৌলিক চাৰ্যাকবাদ নিশ্চয়ই বলতে চেয়েছিল যে, বিশুদ্ধ বুদ্ধি দিয়ে দর্শন গড়া চলবে না, পরমসত্তা বুদ্ধির মুখাপেক্ষী নয়, শুদ্ধ-বুদ্ধির দাবি মানতে বাধ্য নয়। আগেই বলেছি, প্ৰেতকার্যের অন্তঃসারশূন্যতা দেখাতে গিয়ে চাৰ্যাকপন্থী সূক্ষ্ম দার্শনিক যুক্তির অবতারণা করতে চাননি; বরং দৈনন্দিন কর্মজীবনের কষ্টিপাথরে ঘষে দেখাতে চেয়েছেন, এসব ব্যাপার স্রেফ লোকঠকানে ধাপ্লাবাজি। মৌলিক চাৰ্বাকদর্শনের এই শুদ্ধবুদ্ধিবিদ্বেষ হয়তো কালক্ৰমে, ফলাও হয়ে, ব্যাপ্তিখণ্ডনে -অনুমান মাত্রকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টায় – পরিণত হয়েছিল। মাধবাচার্যের গ্রন্থে হয়তো তারই বর্ণনা। তাহলে মানতেই হবে, ভারতবর্ষেবস্তুবাদ এমন পথে অগ্রসর হতে চেয়েছিল যো-পথে এগুলো বস্তুবাদের ঠিক বিপরীতে, অর্থাৎ চরম ভাববাদে, গিয়ে পড়বার সম্ভাবনা। বস্তুত, কডাওয়েল দেখিয়েছেন, শ্ৰেণীসমাজের দর্শনের পক্ষে এই মারাত্মক সম্ভাবনা থেকে যায়; অধ্যাত্মবাদ শেষ পৰ্যন্ত গিয়ে ঠেকে যান্ত্রিক বস্তুবাদে, বস্তুবাদ ভাববাদে। কড্ওয়েল এই কথার উদাহরণ দেখিয়েছেন সাম্প্রতিক য়ুরোপীয় দার্শনিক পরিস্থিতি থেকে; একদিকে হেগেলের অধ্যাত্মবাদ পরিণত হতে চেয়েছে যান্ত্রিক বস্তুবাদে এবং অপরদিকে বৈজ্ঞানিকদের যান্ত্রিক বস্তুবাদ পরিণত হতে চেয়েছে চরম অধ্যাত্মবাদে। এই বিপরীত-পরিণতির আসল কারণ, কডাওয়েল দেখিয়েছেন, শ্ৰেণীবিভক্ত সমাজের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব। প্ৰাচীন ভারতের শ্রেণীবিভক্ত সমাজেও যে এই ঘটনার পুনরুক্তি থাকবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এবং ঘটেছিলও ভাই। একদিকে চাৰ্যাকদের বস্তুবাদ এমন পথে অগ্রসর হতে চেয়েছিল যেপথের চরম পরিণতি ভাববাদ ও সন্দেহবাদ-এ! অপর পক্ষে, ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ যে যুগে যুগে কেমনভাবে চরম ভোগবাদ ও জড়বাদে পরিণত হয়েছে, তার বহুল দৃষ্টান্ত দেশের ইতিহাসে। এখানে দুটি দৃষ্টাস্তের উল্লেখ করা যায়। প্ৰাচীনকালে বৈদিক অধ্যাত্মবাদের অপর পিঠে ছিল ক্রিয়াকাণ্ডের চরম পার্থিবতা, মধ্যযুগে বাংলাদেশে বৌদ্ধ অধ্যাত্মবাদ তন্ত্র, সহজিয়া প্ৰভৃতি চূড়ান্ত পাথিবিতায় পর্যবসিত হয়েছে!
চাৰ্যাকদের কথায় ফেরা যাক। বিশুদ্ধ তর্ক অপ্ৰতিষ্ঠ। অতএব, এই জড় জগতের দুৰ্নিবার যাথার্থ্যকে তর্কবলে উড়িয়ে দেওয়া কোনো কাজের কথা নয়। অপরপক্ষে, স্বৰ্গ নরক বা পারলৌকিক আত্মার কথা হাজার তর্কবলেও প্ৰমাণ করা অসম্ভব। মানতে হবে এই পৃথিবীই একমাত্র সত্য, মাটি-জল-আগুন-বাতাস দিয়ে তৈরি এই পৃথিবী। চাৰ্বাকপন্থী পঞ্চভূতের পঞ্চম ভূতকে-আকাশ বা ব্যোমকে-সত্য বলে মানেন না, কেননা আকাশ ইন্দ্ৰিয়গ্ৰাহস্থ নয় এবং ইন্দ্ৰিয়বেদনা বা অভিজ্ঞতাই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। এই পৃথিবীর চরম সুখই আসল স্বৰ্গসুখ, এই পৃথিবীর চরম যন্ত্রণাই আসল নিরকযন্ত্রণা। মোক্ষ জিনিসটে দেহচ্ছেদেরই নামান্তর। বলাই বাহুল্য, চাৰ্বাকপন্থী দেহের অতীত আত্মা বলে কোনো জিনিস মানেন না। ওরফে তাদের নাম তাই দেহাত্মবাদী। তারা বলেন, দৈনন্দিন জীবনে মানুষ প্ৰতি পদেই দেহাত্মবাদে স্বতঃপ্ৰবৃত্ত আস্থা দেখিয়ে থাকে। মানুষ বলে; “আমি স্থূল”, “আমি কৃশ”, “আমি কৃষ্ণ”। অর্থাৎ, “আমি” জিনিসটা স্থূল, কৃশ, কৃষ্ণ প্রভৃতি দৈহিক লক্ষণ ছাড়া আর কিছুই নয়। “আমার দেহ”, এ শুধু কথার কথা, যেন “দেহ” আর “আমি” দুটো আলাদা জিনিস। এ-রকম কথার কথা, যেন “দেহ” আর “আমি” দুটো আলাদা জিনিস। এ-রকম কথা তো আমরা কতই বলে থাকি; যেমন ধরুন—“রাহুর মাথা”। আসলে মাথাই তো রাহুর সর্ব্বস্ব-মাথা বাদ দিলে রাহু বলে আর কী বাকি থাকবে? ঠিক সেই রকমই; “আমার দেহ”। দেহই আমি এবং আমিই দেহ।
প্রশ্ন ওঠে : তাহলে চেতনা বলে জিনিসটা আসলে কী? চাৰ্বাকপন্থী বলেন, চেতনা জিনিসটে কোনোরকম পারলৌকিক আত্মার বিকাশ মোটেই নয়। তাই বলে চেতনা জিনিসটাকে উড়িয়ে দেবার দরকারও নেই; জড়ের উপর তার আবির্ভাব, জড়ের দরুন তার আবির্ভাব, তবু আবির্ভাব হিসেবে অপূর্ব। তাই তার মধ্যে নতুন গুণের লক্ষণ, সে গুণ জড়মাত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না। আশ্চৰ্য সরল উদাহরণ দিয়ে তঁরা ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিতে চান : কিশ্বাদিভ্যঃ সমেতেভ্যো দ্রব্যোভ্যো মদীশচক্তিবৎ! কিথ (সুরাবীজ) ইত্যাদি। কয়েকটি দ্রব্য একত্র মেশানোর ফলে যেরকম মদশক্তির আবির্ভাব হয়, ঠিক সেই রকমই। কিংবা, আর একটি এইরকম সরল উদাহরণ চাৰ্বাকপন্থীদের নামে প্ৰচলিত আছে : পান, চুন, খয়ের, সুপুরি -এগুলোর কোনোটার মধ্যেই টুকটুকে লাল রঙ নেই, অথচ এগুলি দিয়ে পান। সেজে মুখে দিলে পর ঠোঁটদুটি টুকটুকে লাল হয়ে যায়। লাল রঙ এল কোথা থেকে? এ রঙ পান-চুন-খয়ের-সুপুরি ছাড়া কিছুই নয়, অথচ পান-চুন-খয়েরসুপুরির উপর এক অপূর্ব আবিভােব বই কী। ঠিক তেমনি, ক্ষিতি-আপ-তেজমরুত ছাড়া মানুষ আর কিছুই নয়, তবু এই চতুভূতের এক বিশেষ সমাবেশের ফলেই মানুষের মধ্যে চেতনা বলে ওই অপূর্ব গুণের আবির্ভাব।
আধুনিক বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদী অবশ্য আলোচনা এখানেই শেষ করবেন না। তিনি দেখাতে চেষ্টা করবেন যে, যদিও জড় থেকেই চেতনার উৎপত্তি, জড়ের উপরই তার স্থিতি এবং শেষ পর্যন্ত জড়ের মধ্যেই তা বিলীন হয়ে যায়, তবুও জড়ের উপর তার যে প্রভাব, সে প্রভাবকেও অগ্ৰাহ করবার কোন উপায় নেই। কিন্তু তাই বলে সত্তার দিক থেকে চেতনার বা চিন্তার দাবিই চরম দাবি নয়; বস্তুসত্তা ন্যায়শাস্ত্রের মুখাপেক্ষী নয়, বরং ন্যায়শাস্ত্ৰই বস্তুসত্তার মুখাপেক্ষী। কিন্তু আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ চাৰ্যাকপন্থীদের মধ্যে আশা করা মূঢ়তার পরিচয় হবে, তারা যে সমাজের দার্শনিক সেই সমাজের প্ৰতিচ্ছবিই তাঁদের দর্শনে।
এই কথা বিশেষ করে মনে রাখা দরকার চাৰ্যাকপন্থীদের সুখসর্বস্ব নীতিবাদ সম্বন্ধেও। চাৰ্বাকপন্থী বলেন, জড়াজগৎই যেহেতু একমাত্র সত্য সেইহেতু ইহজগতের ভোগমুখই মানুষের একমাত্র পুরুষাৰ্থ। দেহ একবার ভস্মীভূত হলে পুনরাগমনের আর সম্ভাবনাই নেই, অতএব যতদিন বাঁচা যায়, সুখে করে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে সুনীতি সম্বন্ধে এই সুখসর্বস্ব মতবাদ। কিন্তু বস্তুবাদের একমাত্র অনুসিদ্ধান্ত নয়। বস্তুত, আধুনিক বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ এমনতর কথা মোটেই বলে না। তবু চাৰ্বাকপন্থীর সমসাময়িক সমাজের ছবি মনে রাখলে এই সুখাবাদের ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে। মনে রাখতে হবে, এ মতবাদের প্ৰচলন হলো বৈদিক যুগের ঠিক পরেই, পুরোহিত শ্রেণী তখন অনেকাংশে দেশের শাসক-সম্প্রদায়, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই চাৰ্বাক্যবাদের মূল প্রেরণা। ফলে, পুরোহিত যদি বলেন; ধার করে হোক আর যেমন করেই হোক, পিতৃশ্ৰাদ্ধের দিন পুরোহিত ভোজন করাতে ভুললে চলবে না, তার উত্তরে, চাৰ্বাকের পক্ষে বলে বসাই স্বাভাবিক : ধার করেই হোক আর যেমন করেই হোক, নিজের পেটটা আগে ঠাণ্ডা রাখাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ! বিপক্ষদল তর্ক করতে পারেন : এ পৃথিবী শুধু দুঃখময়, তাই এখানে ভোগান্বেষণ করতে গেলে শেষ পর্যন্ত দুঃখের জালেই জড়িয়ে পড়তে হবে। চাৰ্বাকপন্থী তার উত্তরে বলেন : মাছ খেতে গেলে গলায় কাঁটা বেঁধবার ভয় নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তাই বলে কি মাছ খাবার চেষ্টাই করবে না?
এ কথা ঠিক যে, শুধু এইটুকু বললেই চাৰ্যাকদের মুখসর্বস্ব নীতিবাদের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দেওয়া হয় না। বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের মতে মুখসর্বস্ব নীতিবাদ শুধু সেই শ্রেণীরই মুখপত্র হতে পারে, যে-শ্রেণী সমাজে মুখের অধিকার পেয়েছে। মার্কস-এর পত্রগুচ্ছ দ্রষ্টব্য। যদি তাই হয়, তাহলে চাৰ্বাকদর্শনের পেছনে সুখসম্ভোগের অধিকারী কোন শ্রেণীকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব? চাৰ্যাকদর্শনকে জনগণের দর্শন বলেছি। তাহলে এই নীতিবাদ এল কোথা থেকে? এই নীতিবাদ বস্তুবাদমাত্রেরই অনুসিদ্ধান্তু তো নয়।
বস্তুত, শ্রেণী সংগ্রামের দিক থেকে চাৰ্বাকদর্শনের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে যাওয়া দুঃসাহসের কথা। তার কারণ এ নয় যে, চাৰ্বাকদর্শনে শ্রেণী সংগ্রামের প্ৰতিচ্ছবি অস্পষ্ট। তার আসল কারণ এই যে, প্ৰাচীন ভারতীয় সমাজে শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাসটুকু অত্যন্ত অস্পষ্ট, কেননা আধুনিক ঐতিহাসিকেরা এ এ বিষয়ে পৰ্যাপ্ত গবেষণা করেননি। তাই দর্শনের ছাত্রকে এগুতে হয়। উলটো দিক থেকে; সামাজিক ইতিহাসের পাশাপাশি দর্শনের ইতিহাসকে বোঝাবার মতো মালমশলা নেই বলে দর্শনের ইতিহাসে শ্রেণীসংগ্রামের যে স্পষ্ট প্ৰতিচ্ছবি পাওয়া যায়। তাকেই প্ৰধান সুত্র বলে মেনে নিয়ে সমাজের বিস্মৃত ইতিহাস থেকে শ্রেণী সংগ্রামের কথা খুড়ে বের করবার আশায়। নইলে যে দর্শনের ইতিহাস খামখেয়ালের দুৰ্বোধ্য পরম্পরা হয়েই থেকে যায়।
দর্শন জিনিসটে ব্যক্তিগত দার্শনিকদের খেয়ালী চিন্তা নয়, নৈর্ব্যক্তিক সত্যাম্বেষণাও নয়। সংস্কৃতির অন্যান্য অঙ্গের মতো দর্শনের ইতিহাসেও সামাজিক ইতিহাসেরই প্ৰতিচ্ছবি, এবং সমাজের ইতিহাস যেহেতু শ্রেণীসংগ্রামেরই ইতিহাস-সেইহেতু দার্শনিক মতবাদমাত্রই শ্রেণী:স্বার্থের রঙে রঞ্জিত। প্ৰত্যেক সমাজেরই একদিকে শোষক-শাসক শ্রেণী এবং অপরদিকে শোষিত শ্রেণী। শোষক শ্রেণী সংখ্যায় স্বল্প বলেই শাসিত শ্রেণীকে মোটামুটি জনগণ বলে উল্লেখ করা যায়। লোকোত্তর দর্শন শাসক শ্রেণীর দর্শন, কেননা লোকোত্তরে শাসিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারলে লোকায়তের হাজার গ্লানি তুচ্ছ ও নশ্বর বলে বুঝিয়ে দেওয়া যায়, জনগণকে নিরাপদ, নিরুপদ্রব করে রাখা যায়। লোকায়তিক দর্শন জনগণের দর্শন, কারণ জনগণকে খেতে হয়। গতির খাটিয়ে-পরান্নে ভূরিভোজন তাদের কপালে নেই- এবং গতির খাটিয়ে খেতে হলে বাস্তব পৃথিবীর দুৰ্নিবার যাথার্থ্য নিয়ে তর্ক করবার উপায়ও থাকে না, মেজাজও না। লোকায়তিক দর্শন জনগণের স্বার্থে উদ্দীপ্ত, শাসক শ্রেণীর শোষণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হলে মানতেই হয় শোষণের গ্লানিতে ভরা এই মাটির পৃথিবী স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, মানসিক ধারণামাত্ৰও নয়। অবশ্য জনগণ আর তাদের দাবি কোনো বিশেষ সমাজের একচেটিয়া লক্ষণ নয়, তবুও লোকায়তিক দর্শন প্রত্যেক যুগে প্রসারলাভ করতে পারেনি। কারণ একটি বিশেষ যুগের দর্শনে শুধু সেই শ্রেণীর কথাই প্ৰতিফলিত হয় যে-শ্রেণী সমাজব্যবস্থার মধ্যেও অগ্রণী হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফরাসী বিপ্লবের সময় জনগণ এগিয়ে এসেছিল। উদীয়মান বুর্জোয়া শ্রেণীর পাশাপাশি, সে যুগের ফরাসী দর্শনে তাই বস্তুবাদের অমন প্ৰতিপত্তি। আজকের পৃথিবীর এক বিরাট দেশে জনগণ নতুন পৃথিবী গড়বার পণ করেছে, তাদের কাছে তাই বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদই একমাত্র দর্শন।
য়ুরোপীয় সভ্যতার আলোচনায় ওই তথ্য শুধু অভ্রান্ত নয়, দর্শনের ইতিহাসকে বোঝাবার একমাত্র উপায়। কেননা অন্য যে-কোনোভাবেই চেষ্টা করা যাক না কেন, দর্শনের ইতিহাস শেষ পর্যন্ত হয় ব্যক্তিগত মানুষের খেয়ালী চিন্তার অর্থহীন পরম্পরা, আর না-হয় হেগেলীয় ব্রহ্মের দুৰ্বোধ্যতম লীলাখেলার কাল্পনিক উপাখ্যান হয়ে থাকে। এই অভিজ্ঞতার আলোয় দেশের দর্শনকে বুঝতে পারার আশা নিশ্চয় দুরাশা নয়। কারণ এ দেশ আমার দেশ হলেও এমন কিছু সৃষ্টিছাড়া আজব দেশ নয়। অথচ সুধীসমাজে। ভারতীয় দর্শনের যে আলোচনা আজও প্রচলিত, তা নেহাতই ভাবালুতার ভারে ভারাক্রান্ত, ভ্ৰান্ত স্বাদেশিকতার বিড়ম্বনায় বিকৃত। কিন্তু বিপদ এই যে, ঐতিহাসিক তথ্যের সম্বল অতি স্বল্প, এবং সেইটুকুর উপর নির্ভর করে শ্রেণী-সংগ্রামের দিক থেকে ভারতীয় দর্শনের ব্যাখ্যা দিতে যাওয়া দুঃসাহস। ভরসার কথা শুধু এইটুকুই যে, এ-আলোচনার ভুলভ্রান্তি যোগ্যতার ব্যক্তিকে যোগ্যতম আলোচনায় উদ্দীপ্ত করতে পারে এবং তিনি ভারতীয় দৰ্শন নিয়ে বৈজ্ঞানিক আলোচনার পথ খুলে দিতে পারেন।
প্ৰথম কথা হলো চার্বাকদর্শনের কাল নিৰ্ণয়। এ দর্শনের উপর কোনো যুগে কোনো সম্পূর্ণ গ্ৰন্থ রচিত হোক আর নাই হোক, বিশেষ কোনো ব্যক্তি এ দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা বা প্ৰধান প্রচারক হোন বা না-হোন, এ কথায় কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে, এই দর্শন এককালে আমাদের দেশে রীতিমত শোরগোল শুরু করেছিল এবং কালক্রমে এ দর্শনকে দেশের বুক থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে ফেলবার চেষ্টাও নিশ্চয়ই হয়েছিল। কোন যুগে প্রচারিত হয়েছিল। এই দর্শন? নানান প্ৰাচীন গ্রন্থে লোকায়তিক দর্শনের উল্লেখ পাওয়া যায়। প্ৰাচীনতম বৌদ্ধ গ্রন্থে, এমন-কী মহাভারতে ও উত্তর উপনিষদে, এ মতবাদের কথা আছে! এই সাক্ষ্যগুলির উপর নির্ভর করে আধুনিক পণ্ডিতেরা (রাধাকৃষ্ণন, গার্বে ইত্যাদি) প্ৰমাণ করেন যে, বৈদিক যুগের ঠিক পরে-আনুমানিক খ্ৰীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে-দেশে এই দর্শনের প্রচলন হয়েছিল। ভারতীয় সভ্যতার এই সময়টা ছিল যুগসন্ধির যুগ। রাজনৈতিক ও সামাজিক আলোড়নের যেন শেষ নেই-সেই আলোড়নের ঢেউ যে দর্শনের মতো তথাকথিত নৈর্ব্যক্তিক রাজত্বেও এসে লাগবে, তাতে বিস্ময়ের অবকাশ নেই। এমন-কী শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণনের মতো ভারতীয় দর্শনের আধ্যাত্মিক ঐতিহাসিক এ কথা অস্বীকার করতে চান না। কিন্তু যে করে হোক একটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা তিনি দেবেনই দেবেন। ফলে সমস্ত ব্যাপারটাই অর্থহীনতায় অদ্ভুত হয়ে দাঁড়িয়েছে।
“লোকাচার আর তন্ত্রমূলক পুৱানো ধর্মবিশ্বাসকে খণ্ডন করবার ব্যাপারে এই বস্তুবাদের অবদান অনেকখানিই ছিল। চাৰ্বাক্যমতের মতো বিস্ফোরক শক্তির সাহায্যে বহু শতাব্দীর অন্ধবিশ্বাসকে যদি ঝাকুনি দেওয়া না হতো, তাহলে দীর্ঘ যুগের সমর্থন-লব্ধ তখনকার আচার-বিচারকে উদার-পন্থা অনুসারে সংস্কার করবার চেষ্টা বিফল হতে বাধ্য হতো। বস্তুবাদ ঘোষণা করে ব্যক্তির আধ্যাত্মিক মুক্তি, উচ্ছেদ করে আপ্তবাক্যমূলক ব্যবস্থার; বুদ্ধির দাবির কাছে যার সাক্ষি টেকে না, ব্যক্তি তাকে স্বীকার করবে না। বস্তুবাদ হলো মানবাত্মার পক্ষে নিজেকে ফিরে পাওয়া, যা-কিছু বাইরের জিনিস আর বিদেশী তাকেই পরিত্যাগ করা। অতীতের বোঝা এই যুগের শ্বাসরোধ করেছিল। চাৰ্যাকদর্শন তার হাত থেকে মুক্তি দেবার জন্য পাগলের মতো চেষ্টা। বিশুদ্ধ চিন্তার গঠনমূলক চেষ্টাকে ঠাই করে দেবার জন্যে দরকার ছিল গোঁড়ামি দূর করা, এ দর্শন তা করতে সক্ষম হয়েছিল।”
সোজাসুজি বলা যায়। এগুলি নেহাতই স্থূল অসত্য, কেননা চাৰ্যাকবাদ আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ, এর প্রধান উৎসাহ নিছক বুদ্ধির দাবিকে অস্বীকার করবার, এ মতবাদ আত্মার কোনো অস্তিত্বই মানে না। তাই আধ্যাত্মিক আত্মোপলব্ধির কোনোরকম পথ প্ৰদৰ্শন করায় চাৰ্যাকপন্থীর মধ্যে আগ্ৰহ-কল্পনা নেহাতই বাড়াবাড়ি, এবং বুদ্ধির কাল্পনিক পটকাবাজির জন্তে চাৰ্যাকদের মাথাব্যথার কথাটুকু প্ৰায় হাস্যকর। আশা করি, শ্ৰীযুক্ত রাধাকৃষ্ণনের মতো বিদগ্ধ পণ্ডিত এই স্থূল অসত্যগুলিকে নেহাত অলংকারের খাতিরেই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তবুও, অলংকারের খাতিরে এসব কথা মেনে নিলেও, তার প্রধান বক্তব্যটুকু সহজবুদ্ধির কাছে অর্থহীনতায় দুৰ্যোধ্যই থেকে যায়! আসল কথা হলো : বৈদিক যুগের ক্রিয়াকাণ্ড থেকে মানুষের মনকে সরিয়ে নেবার জন্যে এত মাথাব্যথা ঠিক কার? কার মাথাব্যথা উন্মুক্ত বুদ্ধির নির্মল দর্শনের জন্যে পথ পরিষ্কার করে দেবার? ইতিহাসের? নবযুগের? না, ইতিহাসের ক্রমবিকাশের মধ্যে দিয়ে লীলাখেলায় প্ৰমত্ত কোনো হেগেলীয় পরব্রহ্মের? ভাষার ঝঙ্কার দিয়ে, অলংকারের চোখ-ধাধানো কারিগরি করে এই মূল প্ৰশ্নকে ঢেকে রাখা যেতে পারে, কিন্তু এর কোনো মীমাংসা দেওয়া যায় না। বস্তুত ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ছাড়া যুগে যুগে সভ্যতার পরিবর্তনগুলো নেহাতই হেঁয়ালি হয়ে থাকে। হাজার রকম আধ্যাত্মিক গোঁজামিল দিয়েও এগুলির ব্যাখ্যা হয় না।
অথচ অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসের অর্থ প্ৰাঞ্জল। সমাজের কাঠামো নির্ভর করে ধন উৎপাদন ও বণ্টনের ব্যবস্থার উপর। ফলে, এই ব্যবস্থায় পরিবর্তন এলে সমাজের চেহারাও বদলে যায়; পুরোনো শাসক শ্রেণীর পরিবর্তে দেখা দেয় নতুন শাসক শ্রেণী। এবং সংস্কৃতি জিনিসটে যেহেতু শাসক শ্রেণীরই মুখপত্র, সেইহেতুই নতুন সমাজে সংস্কৃতির রূপান্তর চোখে পড়ে।
এই দৃষ্টিকোণ থেকে চাৰ্বাক-দৰ্শনকে বোঝবার মতো খণ্ড ও বিক্ষিপ্তভাবে কিছু মালমশলা জোগাড় করা যাক। তবু সেটুকুর সাহায্যে প্রাচীন ভারতে এই দর্শনের আবির্ভাবের উপর যেটুকু আলোকপাত করা যায়, তার মূল্যও সামান্য নয়।
শ্ৰীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় দেখাতে চাইছেন, প্ৰাচীন বৈদিক যুগে ভারতীয় সমাজে শ্রেণীবিভাগ দেখা দিয়েছিল, তবু শ্রেণী সংগ্রাম প্ৰকট হয়ে পড়েনি। তার কারণ প্ৰাচীন বৈদিক সমাজের অর্থনীতিতে আদিম সাম্যতন্ত্র ছেড়ে আদিম সামন্ত প্রথার দিকে অগ্রসর হবার লক্ষণ। সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি কৃষিসভ্যতার দিকে যত অগ্রসর হয়েছে, শ্রেণীসংগ্ৰামও ততই স্পষ্ট ও ব্যক্ত হয়ে পড়েছে। তাই পদানত জনগণ বা শূদ্র সম্বন্ধে ঋগ বেদে উল্লেখ শুধু এক জায়গায়। পুরুষসুক্তে, এবং এই পুরুষসূক্ত অনেক পণ্ডিতের মতেই আসলে উত্তর কালে রচিত হয়েছে এবং পিগ বেদের মুধ্যে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। পুরুষসুক্তে। শ্রেণীবিভাগের প্রথম প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়া সম্ভব। বৈদিক ঋষি বলেছেন : “সেই বিরাট পুরুষের মুখ থেকে জন্ম হয়েছে ব্ৰাহ্মণের, তার হাত থেকে রাজন্যের, তার উরু থেকে জন্মেছে বৈশ্য এবং তার পা থেকে জন্মেছে। শূদ্ৰ।” আবার, “ইন্দ্ৰ আর অগ্নি জন্মেছে তার মুখ থেকে- তার পা থেকে পৃথিবী বা মৃত্তিকা।” অর্থাৎ, জনগণ বা শূদ্রের সঙ্গে মাটির সম্পর্ক যেন নাড়ির সম্পর্ক। এই বর্ণনার মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। আদিম সাম্যাবস্থায় সমস্ত মানুষেরই সামাজিক অবস্থা সমজাতিক ও সদৃশ ছিল, যেন এক অভিন্ন বিরাট পুরুষ। কালক্ৰমে ভারতীয় সমাজ চারটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রথমত, যুদ্ধের দায়িত্ব ও কৃষি উৎপাদনের দায়িত্ব পৃথক হয়ে যায়, উৎপাদনের দিক থেকে উন্নত সমাজের রক্ষাকার্যের জন্যে এ বিভাগ প্রয়োজন ছিল। যোদ্ধার দল নিশ্চয়ই বাহুবলে নিজেদের শাসকশ্রেণী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করছিল। কিন্তু বাহুবলে প্ৰতিষ্ঠাকে আরও মজবুত করবার জন্যে প্রয়োজন হয় ধর্মবল ও যুক্তিবলের প্রতিষ্ঠা। তাই, ক্রমশ এই রাজন্য শ্রেণীর মধ্যে থেকে ব্ৰাহ্মণ বা পুরোহিত শ্রেণীর উদয় হলো-বিশ্বামিত্র প্রভৃতির উপাখ্যানে এই ঐতিহাসিক সত্যের প্রতিচ্ছবি। অবশ্যই, শাসক সম্প্রদায় হিসেবে ব্ৰাহ্মণ ও ক্ষত্ৰিয়ের মধ্যে একতা থাকলেও, স্বাৰ্থ বিভাগের দিক থেকে দুই শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব নিশ্চয়ই ছিল-পরশুরাম ও কর্তবীৰ্যার্জন প্ৰভৃতির উপাখ্যানে তার প্রতিচ্ছবি। এই সমস্ত দিক থেকে প্রাচীন ভারতে শ্রেণী সংগ্রামের ছবি অত্যন্ত জটিল, সন্দেহ নেই। তবু পুরুষস্যক্তে এই যে বহিঃরেখা পাওয়া যায়, তার তাৎপৰ্য স্পষ্ট। একদিকে ব্ৰাহ্মণ-ক্ষত্ৰিয়ের শাসক শ্ৰেণী, ব্ৰহ্ম-তেজ ও ইন্দ্ৰবিক্রমে তারা শাসন-কাজ চালাত; পরের উৎপাদনে চলত তাদের সংসার, তাই মাটির সঙ্গে সম্পর্ক বড় একটা ছিল না। অপরদিকে, শূদ্র বা জনগণ; উৎপাদনের সমস্ত দায়িত্ব তাদের ঘাড়ে, তাই মাটির সঙ্গে তাদের যেন নাড়ির যোগ। সেই বিরাট পুরুষের-সেই আদিম সমজাতিক মনুন্য সমাজের-পায়ের থেকে জন্মেছে। শূদ্র, আর জন্মেছে মাটি, -শূদ্রের অন্তরঙ্গ আত্মীয়। এ কথা ঠিক যে, শ্রেণী সংগ্রামের এই রূপ ভারতীয় সমাজে হঠাৎ একদিন ফুটে ওঠেনি এবং সে রূপ। এত সরলও নয়। তবু এ কথাতেও সন্দেহের অবকাশ নেই যে, বৈদিক যুগের শেষেরদিক থেকে ভারতীয় সমাজে শ্রেণীসংগ্রাম প্ৰকট থেকে প্রকটতর হতে শুরু করেছে, কেননা এই সময়টায় দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল, ভারতবর্ষে “এশিয়াটিক সামন্তসমাজে’র ভিত পাকাপাকিভাবে গড়ে উঠেছিল। যুগসন্ধির এই সময়ে বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংগ্ৰাম কঠোর ও তীক্ষ্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সব সংগ্রামের মধ্যে ব্ৰাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের শাসক-ভাগ্য ভাগাভাগি করা নিয়ে যে মারামারি, তারই ঐতিহাসিক প্ৰতিচ্ছবি সবচেয়ে বেশি করে পাওয়া যায়। রামায়ণে এই সংগ্রামের ব্ৰাহ্মণ-সংস্করণ, বৌদ্ধ ও জৈন পুঁথিতে তার ক্ষত্ৰিয়সংস্করণ। এই দুটি সংস্করণই যে ভালোভাবে টিকে গিয়েছে, তার কারণ শাসক শ্রেণীর মধ্যে শেষ পৰ্যন্ত স্বার্থের যেন খানিকটা ভাগাভাগি হয়ে গেল।
কিন্তু এই শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্যে শূদ্রদল বা জনগণ বিপক্ষের জয় বা নিজেদের পরাজয় যে নেহাত অসহায়ভাবে মেনে নিয়েছিল, এমন কথা মনে করবার কোন কারণ নেই। বস্তুত এই সংগ্রামের কোনো স্পষ্ট শূদ্ৰ-সংস্করণ ইতিহাসে টিকে না থাকলেও খণ্ডবিক্ষিপ্ত কয়েকটি তথ্য থেকে এটুকু স্পষ্টই বোঝা যায় যে, শূদ্ৰ-শ্রেণীও মাথা চাড়া দিয়ে ওঠবার চেষ্টা মাঝে মাঝে করেছিল, করেছিল বিপ্লব-ঘোষণা। এই বিপ্লবকে পরিপূর্ণভাবে ধ্বংস করা ছাড়াও শাসকশ্রেণী এ বিপ্লবের সমস্ত চিহ্ন ইতিহাস থেকে মুছে ফেলতে চেয়েছে। তবু প্ৰাচীন ইতিহাসে এ বিপ্লবের অস্পষ্ট স্বাক্ষর; ছন্দ্যোগ্য উপনিষদে জনশ্রুতি নামে শূদ্র রাজার বিবরণ, শতপথ ব্ৰাহ্মণে শূদ্র মন্ত্রীদের কথা, মৈত্রেয়ানী সংহিতায় শূদ্র ধনী ব্যক্তির উল্লেখ। গৌতম, আপস্তম্ভ, মনু প্ৰভৃতি ধর্মশাস্ত্রকাররা যে-শূদ্র সম্বন্ধে কিছুদিনের মধ্যে কঠোরতম বিধিনিষেধের ব্যবস্থা করেছিলেন, সেই শূদ্ৰকে নিশ্চয়ই আদর আপ্যায়িত করে রাজা-উজির বানানো হয়নি। তারা যদি রাজা-উজির হয়ে থাকে, তা হলে তা নিছক নিজেদের জোরেই হতে পেরেছিল। তাই এগুলিকে শূদ্রবিপ্লবের খণ্ড বিক্ষিপ্ত স্বাক্ষর বলে গ্রহণ করা যেতে পারে। সংস্কৃতির স্তরে এই বিপ্লবের প্ৰতিচ্ছবিই চাৰ্যাক-দর্শনে। এবং চার্বাক-দৰ্শন তাই প্ৰাচীন ভারতীয় শ্রেণীসংগ্রামের একমাত্র শূদ্ৰ-সংস্করণ। আরও একটা কথা এই স্বত্রে বুঝতে পারা সম্ভব। আগেই বলেছি, সুখসর্বস্ব নীতিবাদ বস্তুবাদের একমাত্র অনুসিদ্ধান্ত হতে বাধ্য নয়; মার্কস-মতে এ নীতিবাদ শুধু তারই মনের কথা হতে পারে, সমাজে যে মুখসম্ভোগের অধিকার পেয়েছে। তাই যে সব শূদ্র রাজা বা শূত্র ধনী ব্যক্তির উল্লেখ ইতিহাসে পাওয়া যায়, তাদের মুখে সুখসর্বস্ব নীতিবাদ কল্পনা করা অসঙ্গত নয়, সমাজে সুখের অধিকারী তারা নিশ্চয়ই হয়েছিল, এবং যেহেতু মূলত তারা শূদ্ৰই, সেইহেতু শূদ্ৰ-শ্রেণীর সাধারণ দর্শনের সঙ্গে তাদের ভোগবিলাসী নীতিবাদ মিশে যাবার প্রচুর সম্ভাবনা।
অবশ্যই একদিক থেকে এ সমস্ত কথাই নিছক অনুমান মাত্র, কেননা নিশ্চিত ও পৰ্যাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য আপাতত যেটকু সংগ্ৰহ করা সম্ভব, তা দিয়ে প্রত্যেকটি কথা প্ৰমাণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু বৈদিক যুগের পরে ব্ৰাহ্মণরা যে একের পর এক ধর্মশাস্ত্র রচনা করে শূদ্রদের নির্মমভাবে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করেছিল, সে কথাটকু নিশ্চয়ই ঐতিহাসিক সত্য। গৌতম, আপস্তম্ভ, মনু থেকে রঘুনন্দন পর্যন্ত এই প্ৰচেষ্টার ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ ও দীর্ঘ। আপাতত তার উল্লেখ না করলেও চলবে। কেবল এই কঠোর থেকে কঠোরতার বিধানপরম্পরা সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন না তুললেই নয়; শূদ্ৰ-বিপ্লবের পুনরুক্তি সম্বন্ধে ভয় না থাকলে শাসক শ্রেণী এমন বিচলিত মনোবৃত্তির পরিচয় দেবে কেন? চাৰ্যাক-দর্শনের উৎপত্তি সম্বন্ধে দেশে যে প্ৰবাদ প্ৰচলিত হয়েছে, তার মধ্যেও এই বিচলিত মনোভাবেরই পরিচয়। শূন্ত্রদের সমাজে দমন করেও, শূদ্রদর্শনের পুঁথি নিশ্চিহ্ন করেও পুরোহিত শ্রেণীর মনে শান্তি ছিল না। কেননা, জনগণ যেন মরেও মরতে চায় না, তাদের লোকায়ন্তিক দর্শন বারবার খণ্ডন করা হলেও এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিশ্চিত হওয়া কঠিন। দুরুচ্ছেদং হি চাৰ্যাকস্য চেষ্টতম। এই দশনকে সম্পূর্ণভাবে গ্ৰাস করবার আশাতে পুরোহিত-শ্রেণী তাই রটিয়ে দিল—সত্যি বলতে কী, ওই ভ্রান্ত দর্শন এককালে আমরাই রচনা করেছিলুম। আসলে দেবতাদের সঙ্গে তখন অসুরদের জোর লড়াই চলেছিল, অম্বরের এমন লড়াই লড়ছিল যে দেবতাদের অবস্থা প্ৰায় টলোমলে। তখন দেবতাদের গুরুদেব বৃহস্পতি এক ফন্দি আঁটলেন। এক ভ্ৰান্ত ও হেয় দর্শন রচনা করে অসুরদের মধ্যে গিয়ে সেই দৰ্শন প্রচার করে দিলেন -এই ভ্ৰান্ত দশনের মোহে পড়ে তারা ভোগ-বিলাসী হয়ে পড়ল, তার চরিত্র হারাল এবং শেষ পর্যন্ত দেবতাদের কাছে হার মানতে বাধ্য হলো।
খোদ দেবতাদের গুরুদেবের ফন্দিফিকির নিয়ে ন্যায়-অন্যায়ের প্রশ্ন তোলা সামান্য মানুষের পক্ষে নিশ্চয়ই শোভা পায় না। পুরোহিত শ্রেণী হয়তো তাই নিশ্চিন্ত ছিল, এ প্রশ্ন কোনোদিন উঠবে না। তা ছাড়া, লোকায়তে বিশ্বাস করলে লড়াইতে হার মানবার ভয় যে কেন, সে যুক্তিও সহজবুদ্ধির কাছে অস্পষ্ট। কিন্তু আসল কথা হলো, এই প্ৰবাদটির মধ্যে ব্ৰাহ্মণ-শ্রেণীর একটি আদশ পদ্ধতির পুনরুল্লেখ পাওয়া যায়। সংস্কৃতির স্তরে ব্রাহ্মণ শ্রেণী বিপক্ষকে শুধু খণ্ডন করেই ক্ষান্ত হয় না, কোনো মতে নিজের শ্রেণীর মধ্যে বিপক্ষকে শুষে নেবার চেষ্টা করে। তাই ভগবান বুদ্ধ দশ অবতারের এক অবতার হয়ে গেলেন। শুধু দর্শনের বেলাতে নয়, ব্রতের বেলাতেও একই পদ্ধতি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখিয়েছেন, কেমনভাবে দেশের ঘোষিত প্ৰচলিত বা মেয়েলি ব্ৰতগুলিকে শাস্ত্রীয় ব্রতের মধ্যে শুষে নেবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই রকম অজস্র উদাহরণ সাহিত্যে শিল্পে দেবদেবীর কল্পনায়-সংস্কৃতির প্রায় সমন্ত ক্ষেত্রেই। অতুলচন্দ্ৰ গুপ্তর সেই ছোট্ট প্ৰবন্ধটির কথা মনে পড়ল : “গণেশ”। “সর্ববিঘ্নহর ও সর্বসিদ্ধিদাতা বলে যে দেবতাটি হিন্দুর পূজা-পার্বণে সর্বাগ্রে পূজা পান, তার ‘গণেশ” নামেই পরিচয় যে তিনি ‘গণ’ অর্থাৎ জনসংঘের দেবতা। এ থেকে যেন কেউ অনুমান না করেন যে, প্ৰাচীন হিন্দুসমাজের যারা মাথা, তার জনসংঘের উপর অশেষ ভক্তি ও প্রীতিমান ছিলেন। যেমন আর সব সমাজের মাথা, তেমনি তারাও সংঘবদ্ধ জন-শক্তিকে ভক্তি করতেন না, ভয় করতেন!…আদিতে গণেশ ছিলেন কর্মসিদ্ধির দেবতা নয়, কর্মবিঘ্নের দেবতা। যাজ্ঞবল্ক স্মৃতির মতে এঁর দৃষ্টি পড়লে রাজার ছেলে রাজ্য পায় না, কুমারীর বিয়ে হয় না…বণিক ব্যবসায়ে লাভ করতে পারে না…। এইজন্যই গণেশের অনেক প্রাচীন পাথরের মূতিতে দেখা যায় যে শিল্পী তাকে অতি ভয়ানক চেহারা দিয়ে গড়েছে; গণশক্তির উপর প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার কর্তাদের মনোভাব কী ছিল, তা গণেশের নর-শরীরের উপর জানোয়ারের মাথার কল্পনাতেই প্ৰকাশ।” কিংবা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে-রকম দেখাবার চেষ্টা করেছেন, আদিদেব মহাদেবের কল্পনাটা ব্ৰাহ্মণদের পক্ষে আদিবুদ্ধর কথা আত্মসাৎ করবার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়; ‘খৃষ্টান পাদ্ৰীরা যেমন দীক্ষিত ব্যক্তির মাথায় জল ছিটাইয়া দিয়া দলে টানিয়া লন সেইরূপ ব্ৰাহ্মণের আদিবুদ্ধের গলায় যজ্ঞোপবীতের ফাঁস নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে আপনাদের দলে টানিয়া লইলেন।” তাই চতুর্মুখ ব্ৰহ্মার চারমুখ ভরা বেদ থাকলেও গলায় পৈতে নেই; কিন্তু গাঁজাখোর শিব ভূতপ্রেতের দলে নাচলেও তার গলায় পৈতে! হিন্দুসভ্যতার ইতিহাসে এমনতর দৃষ্টান্তর অভাব একটুও নেই।