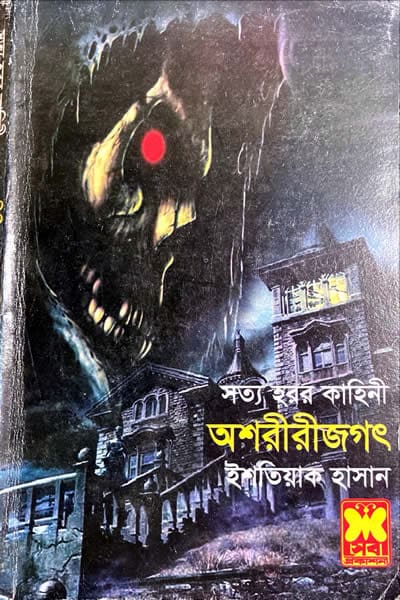- বইয়ের নামঃ অশরীরীজগৎ
- লেখকের নামঃ ইশতিয়াক হাসান
- সিরিজঃ সেবা হরর সিরিজ
- প্রকাশনাঃ সেবা প্রকাশনী বই
- বিভাগসমূহঃ ভূতের গল্প
অশরীরীজগৎ
পাতালকুঠুরী লণ্ডভণ্ড
প্রয়াত হ্যারি প্রাইস পল্টারগাইস্টদের সম্পর্কে বলেছিলেন এরা রীতিমত অভিশপ্ত প্রেতাত্মা, ভয়ঙ্কর এদের আচরণ। সাধারণ ভূতেরাও নানা ধরনের সমস্যা তৈরি করে। কখনও এরা দেখতে ভীতিকর, বদখত, প্রচুর শব্দ করে, তবে এদের মধ্যে অনেকই আছে যারা মানুষের বিশেষ করে যাদের বাড়িতে বা এলাকায় থাকে তাদের ক্ষতি করে না। কখনও কখনও তো রীতিমত বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করে।
কিন্তু পল্টারগাইস্টদের কাছে এসব প্রত্যাশা করা বৃথা। এরা ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে অভ্যস্ত, এমনকী এই আচরণের পেছনে গ্রহণযোগ্য কোন কারণও থাকে না। প্ৰচণ্ড প্রতিহিংসাপরায়ণও। বলা হয় সাধারণ ভূতেরা কেবল কোথাও উদয় হয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেও এরা রীতিমত উপদ্রব চালায়।
নানা ধরনের পরিবেশেই পল্টারগাইস্টদের আনাগোনার খবর পাওয়া যায়। স্বাভাবিকভাবেই সমাধিক্ষেত্রগুলোও এর ব্যতিক্রম নয়।
তবে এর সঙ্গে আবার বিভিন্ন গোরস্থানে দেখা দেয়া নিরপরাধ কিছু প্রেতাত্মাকে গুলিয়ে ফেলবেন না যেন। মেরি কটনের সেই শিশু শিকারদের কথা বলা যেতে পারে। নিজের চার সন্তানসহ গোটা পনেরো শিশুকে হত্যার অভিযোগে ফাঁসি হয় ডারহামের পশ্চিম অকল্যাণ্ডের মেরি কটনের। যেসব গোরস্থান ও সমাধিক্ষেত্রে এই শিশুদের গোর দেয়া হয় সেসব জায়গায় তাদের ভূতের দেখা মেলে। এমনই এক দুর্ভাগা ছোট্ট ভূত একবার গ্রামের পোস্টম্যানকে অনুসরণ করতে থাকে। পরনে ছিল গোর দেয়ার সময়কার পোশাকটি। একপর্যায়ে পোস্টম্যানের পিছু পিছু তার বাড়ি হাজির হয়। তারপর ঢুকে পড়ে ভদ্রলোকের ছোট্ট শিশুটি যে কামরায় ঘুমিয়ে ছিল সেখানে। আতঙ্কিত পোস্টম্যান ও এই দুর্ভাগা ছোট্ট মেয়ের অশরীরীকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে সদাশয় এক মহিলা। ভুতুড়ে এক বাড়িতে বাস করা ওই বুড়ো মহিলা প্রেতাত্মাদের সঙ্গ পেয়ে অভ্যস্ত। মহিলা পরে বলে, ‘অন্ধকার পাতালকুঠুরী খুব ঠাণ্ডা, সেখানে নিঃসঙ্গও ছিল মেয়েটা। ওকে একটু আরাম দেয়ার চেষ্টা করেছি আমি। তোমাকে আর বিরক্ত করবে না সে।’ সত্যি ছোট্ট ওই ভূতকে আর দেখা যায়নি। ধারণা করা হয় বুড়ির ভুতুড়ে বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছিল সে।
এই পল্টারগাইস্টরা সাধারণ শান্ত প্রেতাত্মাদেরও বেশ ঝামেলায় ফেলে। বলা হয় কোন কোন গোরস্থানের পারিবারিক ভল্ট বা পাতালকুঠুরীগুলোতে মারাত্মক ধ্বংসযজ্ঞ চালায় তারা।
এবার যে ঘটনাটি বলব সেটা রেকর্ড করা হয় ইংল্যাণ্ডের সাফোক কাউন্টির স্টেনটন গ্রামের এক সমাধিক্ষেত্র থেকে ১৮১৫ সালে।
একদিন ভল্ট খুলতেই দেখা যায় কাঠের পাটাতনে আটকানো কাঠের ঢাকনি দেয়া কিছু সীসার কফিনের জায়গা বদল হয়ে গিয়েছে। গ্রামবাসীরা ভয় পেয়ে গেল। কফিনগুলো আগের জায়গায় রেখে পাতালকুঠুরী আটকে দেয়া হলো। কিছুদিন পর একজনকে সমাধিস্থ করতে গিয়ে একই সমস্যা চোখে পড়ল গ্রামবাসীর। দু’বছর বাদে যখন আবার খোলা হলো ভল্ট, আরও বড় চমক অপেক্ষা করছিল তাদের জন্য। অন্যান্যবারের মত কফিনগুলো শুধু এলোমেলো অবস্থায়ই নেই, আটজন মানুষ বইতে হয় এমন একটা ওজনদার কফিন ভল্টের দিকে যাওয়া সিঁড়ির ওপর এনে রাখা। কে করল তবে কাজটা?
দু’একজন অতি বুদ্ধিমান দাবি করল পাতাল নদীর জলস্রোতের কারণে এটা হতে পারে। কিন্তু সেরকম কোন আলামত চোখে পড়ল না। তাছাড়া এরকম পানির তোড়েও সীসার কফিন নড়ার কথা নয়।
তবে এ ধরনের ঘটনার সবচেয়ে বড় প্রমাণটি পাওয়া যায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বার্বাডোজে, ক্রাইস্ট চার্চের সঙ্গে যুক্ত ছোট্ট এক গোরস্থানে। দ্বীপটির সবচেয়ে দক্ষিণের বাতিঘরটির কাছেই এর অবস্থান। ব্রিজটাউন থেকে সড়ক পথে দূরত্ব আধ ঘণ্টা।
সাগর সমতল থেকে শ’খানেক ফুট উচ্চতায় ভল্টটি। পাথর কেটে ভেতরে বানানো হয়েছে। এর মেঝে, দেয়াল স্বাভাবিকভাবেই পাথরের। ওটা আটকানো নীল ডেভনশায়ার মার্বেল পাথরের টুকরো বা স্ল্যাব দিয়ে। জিনিসটা এতটাই ভারী যে কয়েকজন লোক লাগে তুলতে।
বার্বাডোজের প্রাচীন কয়েকটি পরিবারের সম্পত্তি এই ভল্ট। ওয়ালরণ্ডদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল এটি। তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কের সূত্র ধরে পায় ইলিয়টরা। রাজার সভাসদের সদস্য ছিল এই পরিবারগুলোর কর্তাব্যক্তিরা। প্রচুর দাস ছিল তাদের। দ্বীপ শাসন করত তারাই।
১৭২৪ সালে বার্বাডোজ কাউন্সিলের সদস্য জেমস ইলিয়ট মারা যান ৩৪ বছর বয়সে। তাঁর দুর্ভাগা স্ত্রী টমাস ওয়ালরণ্ডের মেয়ে এলিজাবেথ স্বামীর দেহাবশেষ নিয়ে আসেন তাঁদের পারিবারিক ভল্টে। পাথরের ফলকে খোদাই করার ব্যবস্থা করেন কয়েকটা বাক্য, ‘সাহসী, পরোপকারী একজন মানুষ ছিলেন তিনি। ১৪ মে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয় তাঁকে। পরিচিত সবাই তাঁর এই অকাল মৃত্যুতে ব্যথিত, পীড়িত।’
১৭২৪ সালে এখানে কয়টা কফিন ছিল তার রেকর্ড ছিল না। তবে শতকের বাকি সময়টা মোটামুটি নতুন কাউকে সমাধিস্থ করা হয়নি। ১৮০৭ সালের জুলাইয়ে গির্জার যাজকের কাছে একটা দরখাস্ত পেশ করা হয়, তাতে ইলিয়টদের আত্মীয়া মিসেস থমাসিনা গডার্ডকে এই ভল্টে সমাহিত করার আবেদন করা হয়। গির্জার পক্ষ থেকে অনুমতি দেয়া হয়।
শ্রমিকরা তখনই অক্ষত সিলগুলো ভেঙে ফেলে। নিগ্রো দাসরা বিশাল মার্বেল পাথরের খণ্ডটা সরাতেই সবার চোখ ছানাবড়া। ভেতরটা শূন্য। ইলিয়ট বা ওয়ালরওদের কারও কফিনই নেই। অনেক তল্লাশি চালিয়েও ওগুলোর খোঁজ মিলল না। যা হোক, মিসেস গর্ডাডকে সমাধিস্থ করার কাজ এতে আটকে থাকল না। ৩১ জুলাই চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন পাতালকুঠুরীতে।
তারপর ভল্টটির মালিকানা পায় চেজ পরিবার। ধনী, ক্ষমতাধর এক পরিবার। ওই সময়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অন্যান্য অভিজাত ইয়োরোপীয় পরিবারগুলোর মত বেশ কিছু বাগান এবং দাসের মালিক ছিল পরিবারটি। ভল্টের প্রবেশ পথের ওপরে চেজ পরিবারের প্রতীকচিহ্ন খোদাই করে দেয়া হলো। ওটা দেখতে পাবেন এখনও।
প্রথম চেজ হিসাবে সমাধিস্থলটিতে গোর দেয়া হয় ম্যারি অ্যানা মারিয়াকে, এলাকার মান্যগণ্য ব্যক্তি টমাস চেজের কিশোরী বোন সে। ১৮০৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে মারা যায় ছোট্ট মেয়েটি। একটা সীসার কফিনে পুরে তাকে আনা হলো। সমাধিস্থ করতে ভল্ট খোলা হলে দেখা গেল মিসেস গডার্ডের কাঠের কফিনটি আগের জায়গাতেই আছে।
১৮১২ সালের ৬ জুলাই পাতালকুঠুরী আবার খোলা হয় টমাস চেজের আরেক বোন ডোরকাস চেজকে কবর দিতে। এবার নিহতের সঙ্গে আসা আত্মীয়-স্বজন ভেতরের অবস্থা দেখে থ হয়ে গেল। অ্যানা মারিয়ার মৃতদেহসহ সীসার কফিনটা খাড়া হয়ে আছে। কফিনের মাথার অংশটা নিচের দিকে। আর যেখানে রাখা ছিল তার উল্টো পাশে আছে এখন। মিসেস গডার্ডের বিশাল কাঠের কফিনটারও যেন হাত-পা গজিয়েছে। জায়গা বদলেছে ওটাও।
হতবাক দলটা কফিনগুলোকে আগের অবস্থানে রেখে ডোরকাস চেজকে সমাধিস্থ করার কাজ সম্পন্ন করল। এবার ভল্টের মুখে মার্বেল পাথরের স্ল্যাবটা রেখে যাজক ও অন্যদের উপস্থিতিতে সিলমোহর মেরে দেয়া হলো।
ওই বছরই আবার খুলতে হলো সমাধিক্ষেত্রটি। এবার টমাস চেজের জন্য। তবে ভেতরে কোন অসামঞ্জস্য পাওয়া গেল না।
১৮১৮ সালে বেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বার্বাডোজ। বেশ কয়েকবার বিদ্রোহ করে কৃষ্ণাঙ্গ দাসরা। সংখ্যায় এত বেশি ছিল যে শ্বেতাঙ্গ-মালিকদের পক্ষে তাদের সামলানো বেশ মুশকিল হয়ে পড়েছিল। ওই সময় মারা যাওয়া শ্বেতাঙ্গদের একজন চেজ পরিবারের এক আত্মীয়া। ১৮১৮ সালের সেপ্টেম্বরের ১৬ তারিখ এখানে গোর দেয়ার জন্য আনা হলো স্যামুয়েল ব্রিউস্টার এমেসকে। তার মৃতদেহ রাখার জন্য ভল্ট খোলা হতেই দেখা যায় ভারী সীসার কফিনগুলোর একটাও আগের জায়গায় নেই। শুধু তাই না, দেখে মনে হচ্ছে ওগুলো প্রচণ্ড ক্রোধে ছুঁড়ে ফেলেছে কেউ।
১৮১৯ সালের ৯ জুলাই মিস থমাসিনা ক্লার্কের মৃতদেহ আনা হয় ভল্টে সমাধিস্থ করত। আবারও চমক। কফিনগুলো মোটেই আগের জায়গায় নেই। যাজক ড. টি. এইচ. অরডারসন এবার বেশ গুরুত্বের সঙ্গে নিলেন বিষয়টিকে। তিনি আরেকটা বিষয় খেয়াল করলেন, সমস্যা মূলত হয়েছে সীসার কফিনে, কাঠের কফিনগুলো মোটামুটি আগের জায়গাতেই আছে।
কৃষ্ণাঙ্গ দাসরা এসে ওগুলোকে আবার ঠিকঠাক করল। এসময়ই একটা বিষয় জানা গেল, ১৮০৭ সালে গোর দেয়া মিসেস গডার্ডের কাঠের কফিনটা টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। ওটাকে বেঁধে মিসেস ক্লার্কের কফিন ও দেয়ালের মধ্যখানে রাখা হলো।
এই পর্যায়ে এসে সত্যি বিচলিত হয়ে পড়লেন চার্চের যাজক এবং চেজ পরিবারের সদস্যরা। তাঁরা বিষয়টি দৃষ্টিগোচর করলেন বার্বাডোজের গভর্নর লর্ড কম্বারমেয়ারের। পেনিনসুলা যুদ্ধে ওয়েলিংটনের অধীনে একটা ক্যাভালরির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি। সালামানকাতে দারুণ বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে পদকও পান। সাহসী এই সৈনিক ঠিক করলেন রহস্যময় এই ঘটনাটা পরীক্ষা করে দেখবেন নিজে উপস্থিত থেকে। তাঁর প্রথমে মনে হচ্ছিল কৃষ্ণাঙ্গ দাসরা এর পেছনে থাকতে পারে। তবে কেন এটা করবে, বুঝতে পারছিলেন না। তাঁর এডিসি মেজর ফিঞ্চসহ নিজেই সমাধিস্থলে উপস্থিত হলেন গভর্নর।
তাঁদের এবং যাজকের উপস্থিতিতে কফিনগুলো সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা হলো, আর ওগুলোর সঠিক অবস্থান একটা কাগজে এঁকে নিলেন মেজর ফিঞ্চ। ওটা সংরক্ষণ করা হলো। ভল্টের মেঝেতে বালু ছিটিয়ে দেয়া হলো। ভারী মার্বেল পাথরের স্ল্যাবটা দিয়ে আটকে দেয়া হলো প্রবেশদ্বার। রাজমিস্ত্রী ও সরকারি লোকেরা নরম সিমেন্টে বেশ কিছু গোপন সিল এবং চিহ্ন দিয়ে রাখল।
গভর্নর লর্ড কম্বারমেয়ারের ইচ্ছা ছিল চেজ পরিবারের কেউ মারা গেলে তবেই ভল্ট খুলবেন। তবে নয় মাস পেরিয়ে গেলেও যখন মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া গেল না তখন কম্বারমেয়ার পাতালকুঠুরীতে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নিলেন।
এলড্রিজদের বাগানে ১৮২০ সালের ১৮ এপ্রিল একটা মিটিং হলো। গির্জার পাশেই জায়গাটি। কোন কোন সূত্রের দাবি ভল্টের ভেতরে প্রচণ্ড একটা শব্দ শোনার গুজবেই এই সভা। অন্য সূত্রের মত, গভর্নরসহ বাকি লোকজন এতটাই কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলেন যে আর অপেক্ষা করার ধৈর্য তাঁদের ছিল না।
ওই দিনই গভর্নর, এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তি নাথান লুকাস, মেজর ফিঞ্চ, যাজক এবং এই বিষয়ে আগ্রহী রবার্ট বউচার ক্লার্ক ও রোলাণ্ড কটন হাজির হলেন পাতালকুঠুরীর সামনে। প্রথমেই গত বছরের জুলাইয়ে রেখে যাওয়া গোপন সব সিল ও চিহ্ন পরীক্ষা করে দেখা গেল ওগুলো অক্ষতই আছে। তেমনি সমাধিস্থলটির প্রবেশদ্বারে কারও হস্তক্ষেপের কোন চিহ্নই মিলল না। কম্বারমেয়ার ও তাঁর সঙ্গীরা নিশ্চিত হলেন যে কারও পক্ষেই সমাধির ভেতরে ঢোকা সম্ভব হয়নি। ‘ঘাসের একটা ডগা কিংবা অন্য কিছুও ঢোকার সুযোগ ছিল না,’ পরে তাঁর ডায়ারিতে লেখেন নাথান লুকাস, ‘কোন ধরনের চাতুরী কিংবা ষড়যন্ত্রের সম্ভাবনাই নেই।’
তখন দুপুর। পাশের বাগানে কঠোর পরিশ্রম করে আসা কৃষ্ণাঙ্গ শ্রমিকেরা কাজ সেরে ফিরছিল। তাদের আট- দশজনকে নেয়া হলো গোরস্থানে ভল্ট খোলার কষ্টসাধ্য কাজটি করার জন্য।
পাতালকুঠুরীতে ঢুকতেই সেখানে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা টের পাওয়া গেল। বিশাল সীসার কফিনগুলো, যেগুলোর কোন কোনটা তুলতে ছয়জন মানুষের প্রয়োজন, ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে ভল্টের ভেতরে। দেয়ালে গিয়ে আছড়ে পড়েছে কয়েকটা। কোনটা খাড়া হয়ে আছে। কাঠের কফিনগুলো তাদের আগের অবস্থানেই আছে। মিসেস গডার্ডের জোড়া লাগানো কফিনটাও নড়ানো হয়নি। মেজর ফিঞ্চ ভল্টের ভেতরের কফিনের এবারের অবস্থানও এঁকে নিলেন। রহস্যময় এই ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ এক দলিল হয়ে থাকল যা।
গোটা পাতালকুঠুরী এরপর ভালভাবে পরীক্ষা করা হলো। গত জুলাইয়ে যখন আটকানো হয় ভল্টটা তখন যে বালু ফেলা হয়েছিল তাতেও কোন চিহ্ন মিলল না। ভেতরের প্রতিটি দেয়াল পরীক্ষা করলেন লুকাস। একজন রাজমিস্ত্রী এরপর ওই দেয়ালগুলো আবার তন্ন তন্ন করে খুঁজল। কিন্তু পাথরের মধ্যে ফাঁপা কোন জায়গাই পাওয়া গেল না।
কেউ একজন তখন বলল একটা ভূমিকম্পই এর জন্য দায়ী। কিন্তু ভূমিকম্প, যেটার প্রভাবে কিনা সীসার ভারী সব কফিন ছিটকে গিয়ে দেয়ালে পড়েছে, সেটা নিশ্চয় যেনতেন কিছু নয়। এতে গোটা বার্বাডোজের না হলেও অন্তত এই এলাকার সব বাড়ি-ঘর ধূলিসাৎ হওয়ার কথা। তাই এই তত্ত্বটা ধোপে টিকল না। যেমন টিকল না পানির স্রোত বা অপ্রত্যাশিত পাতাল বন্যার তত্ত্বটা। কারণ ১৮২০ সালের ১৮ এপ্রিল ভল্টের ভেতরটা ছিল শুকনো খটখটে। তাছাড়া এই ঘটনার জন্য প্রচণ্ড পানির তোড় প্রয়োজনে। তাই যদি হবে, তাহলে কাঠের কফিনগুলো আগের জায়গায় থাকল কীভাবে?
নাথান লুকাস লেখেন, তিনি এবং উপস্থিত বাকি সবাই রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে যান ব্যাপারটায়।
‘নিঃসন্দেহে চোরদের এতে কোন ভূমিকা নেই,’ নাথান লেখেন, ‘তেমনি কৃষ্ণাঙ্গদেরও হাত থাকা অসম্ভব। কারণ কুসংস্কারের কারণেই গোরস্থানের ভেতরে ঢুকতে ভয় পায় তারা। কিন্তু এখানে একটা অস্বাভাবিক শক্তির উপস্থিতি টের’ পাওয়া গিয়েছে। আমি নিজে এর সাক্ষী।’
একটা সরকারি রিপোর্ট প্রকাশের পর গভর্নরের এই তদন্ত নিয়ে গোটা বার্বাডোজে দারুণ আলোড়ন পড়ে যায়। চেজদের অনুরোধে ভল্ট থেকে সব কফিন সরিয়ে অপর একটা গোরস্থানে সমাহিত করা হয়। পরিত্যক্ত হয় ভুতুড়ে এই পাতালকুঠুরী। সরকার ওটাকে খুলে দেয়ার নির্দেশ দেন। এখন ওটা খোলাই আছে।
যদিও ঘটনাটা ওই এলাকায় তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে, এর ব্যাপারে সংবাদপত্রে কিছু আসেনি। তেমনি চার্চের গোর রেজিস্টারেও এ সম্পর্কে কিছু লেখা হয়নি। অথচ ওটা নথিবদ্ধ করেন যাজক অরডারসন। এই কাহিনীটা অনেকেই বলেছেন, তবে নাথান লুকাসের ডায়ারির বর্ণনাটাই সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য।
অনেকটা এ ধরনের আরেকটি ঘটনার কথা শোনা যায় বাল্টিক সাগরের ওয়েসেল দ্বীপের আরেনসবার্গ গোরস্থানে। ওটা ১৮৪৪ সালে। বার্বাডোজের ঘটনার সঙ্গে এর বেশ মিল আছে।
এক নারী ও তার দেবরের মধ্যে ছিল খুব খারাপ সম্পর্ক। একই বাড়িতেই থাকত তারা। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই ঝগড়া ছিল প্রাত্যহিক ব্যাপার।
প্রাত্যহিক ব্যাপার। অদ্ভুত ঘটনা, কয়েকদিনের ব্যবধানে মৃত্যু হয় তাদের। মৃত্যুশয্যায় দেবর বলে যায় ভাবীর সঙ্গে একই সমাধিক্ষেত্রে যেন গোর দেয়া না হয় তাকে। কারণ অন্য দুনিয়ায়ও তাদের ঘৃণার বিন্দুমাত্র উপশম হবে না বলে ধারণা তার। কিন্তু এই কথাকে পাত্তা না দিয়ে পারিবারিক ভল্টে ভাবীর পাশেই সমাধিস্থ করা হলো দেবরটিকে। তারপরই সিল করে দেয়া ভল্টের ভেতর থেকে ভয়ঙ্কর এক শব্দ শোনা গেল। এতটাই বীভৎস ছিল মানুষের চিৎকার আর ধাতব পদার্থ ঠোকাঠুকির ওই শব্দ যে ভল্ট খুলে দেখতে বাধ্য হলো পরিবারের সদস্যরা। দুটো কফিনই শুধু যে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে তা নয়, দুটোর অবস্থান এমন জায়গায় যে মনে হচ্ছে একটা আরেকটার সঙ্গে লড়াইয়ে মত্ত ছিল। তাদের ঠিকঠাক করে ভল্ট আটকানোর পর আবার একই ঘটনা ঘটল। তবে ভদ্রমহিলার বুড়ো স্বামী জীবনের শেষ কয়টা দিন তাঁর ম্যানর হাউসে শান্তিতেই কাটান বিচক্ষণ এক সিদ্ধান্তের কারণে। ভাই আর স্ত্রীর কফিনের মাঝখানে শক্তিশালী একটা দেয়াল তুলে দেন। এতে গোটা ভল্টেই শান্তি ফিরে আসে।
কৃষ্ণাঙ্গদের বিশ্বাস জাম্বি নামের এক অশুভ আত্মা কফিনের এই ঝামেলার জন্য দায়ী। ওয়াকিং ডেড বা জোম্বি শব্দটা থেকেই জাম্বির উৎপত্তি। এ ধরনের অতৃপ্ত আত্মারা রাতের বেলা ঘুরে বেড়ায় আর নানা ধরনের ঝামেলা পাকায়। অবশ্য চেজদের ওই ভল্টের ঘটনার জন্য জাম্বিরাই দায়ী তার কোন প্রমাণ নেই।
লাল ক্ষত
সেন্ট যোসেফ, মিসৌরি, আমেরিকা। তরুণ সেলসম্যান তার হোটেল কামরায় বসে বসে কোম্পানির অর্ডার ফর্মগুলো পূরণ করছে। জানালা গলে সকালের উজ্জ্বল সূর্যালোক ভিতরে ঢুকছে। মনটা খুব ফুরফুরে তার আজ। তার জন্য সব দিক থেকেই চমৎকার এক দিন এটা। নতুন গ্রাহকদের তালিকা অফিসে পৌছার পর বস কতটা খুশি হয়ে উঠবে এটা ভেবে এখনই হাসি একান-ওকান হচ্ছে। একটা নতুন সিগার ধরিয়ে দোয়াত থেকে কলমটায় আবার কালি ভরে নিল। এসময়ই হঠাৎ আবিষ্কার করল কামরাটাতে এখন আর একা নেই সে।
ডান পাশের টেবিলটায় কেউ একজন বসে আছে। বিস্মিত হয়ে ঘুরে তাকাতেই বোন অ্যানির সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। তার দিকে উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে আছে।
খুশির চোটে ভয়ানক সেই স্মৃতিটাও বেমালুম ভুলে গেল। পুরো বিষয়টা এতটাই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে তার কাছে যে, লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে উঠল, ‘ওহ, অ্যানি, বোন আমার।’ কিন্তু যখনই নাম ধরে ডাকল, সুবেশী, অপরূপা তরুণীটি অদৃশ্য হলো।
তখনই যেন বাস্তবে ফিরে এল তরুণ। অ্যানিকে তো দেখার কোন সুযোগই নেই তার। বোনকে যেখানটায় দেখেছিল সেদিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কিন্তু তাকে পরিষ্কারভাবে দেখেছে সে। সে যেরকম সুন্দরী ছিল ঠিক তেমনটাই আছে। কিন্তু এখন ১৮৭৬, নয় বছর আগে ১৮৬৭ সালেই কলেরায় মারা গেছে অ্যানি। হোটেলের কামরাটায় একাকী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোটা বিষয়টা আরেকবার ভাবল। হঠাৎ মনে হলো বোনের মধ্যে একটা অস্বাভাবিকতা চোখে পড়েছে তার। পোশাক, চুলের কাট এমনকী চেহারার অভিব্যক্তি শেষবার যেমন দেখেছে ঠিক তেমনটিই। তবে চমৎকার গড়নের মুখে একটা অস্বাভাবিকতা চোখে পড়েছে, জীবত থাকা অবস্থায় যা দেখেনি। ডান চোখের ওপরে কপালে একটা গাঢ় লাল ক্ষতচিহ্ন।
‘বাবা, এটা পাগলের প্রলাপ মনে হতে পারে। কিন্তু সত্যি বোনকে দেখেছি। তুমি এখন যতটা দূরে আমার ঠিক ততটা দূরে বসে ছিল ও আমার থেকে। আমি নিশ্চিত চিলেকোঠায় ওর ট্রাঙ্ক খুঁজলে যে পোশাকটা আজ পরা ছিল সেটা খুঁজে বের করতে পারব। যতই অবিশ্বাস্য শোনাক সে এসেছিল।’
সেন্ট লুইসে বাবার বাড়ির পার্লারে বসে আছে তরুণ বিক্রয় প্রতিনিধি। সে এতটাই হতবাক হয়ে পড়েছে যে কাজ শেষ না করেই পরের ট্রেনে সেন্ট লুইসে চলে এসেছে বাবা মা এবং ভাইকে ঘটনাটা খুলে বলার জন্য। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনা বিশ্বাস করার কোন কারণ খুঁজে পায়নি বাড়ির বাকি লোকজন।
‘শোনো, আমার মনে হয় তোমার মন তোমাকে ধোঁকা দিয়েছে,’ বললেন বাবা, ‘হয়তো কামরার কোন একটা কিছু, বাইরের পরিবেশ কিংবা মানসিক কোন একটা পরিবর্তন তোমাকে বোনের কথা মনে করিয়ে দেয়। এতেই তোমার মনে হয়েছে সত্যি সত্যি হাজির হয়েছে সে। মানুষের জীবনে এ ধরনের ঘটনা ঘটতেই পারে।’
‘বাবা, এটা মোটেই আমার স্মৃতি কিংবা কল্পনা নয়। অ্যানি আমার সঙ্গে ওই কামরাতেই ছিল।’ জোর গলায় বলার চেষ্টা করল তরুণ।
বাবা কেবল হেসে মাথা ঝাঁকালেন। তরুণ নিশ্চিত বাবা তার কথা বিশ্বাস করেননি মোটেই। সম্ভবত ঘটনাটা নিজের মনের মধ্যে চেপে রাখলেই ভাল হত। আসলে প্রিয় বোনকে এত বছর পর দেখে পরিবারের সবার সঙ্গে দেখা করে জানানোর লোভ সামলাতে পারেনি। সবাই-ই যে তাকে ব ভালবাসত। তাহলে সে কী দেখল? অন্যদের বিশ্বাসই বা করাবে কীভাবে?
‘আমি জানি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করোনি, কিন্তু সে এসেছিল,’ আবারও জোর দিয়ে বলল সে, ‘শেষবার .যেমন সুন্দর ছিল এখনও ঠিক তা-ই আছে। শুধু কপালের ওই দাগটা ছাড়া।’
তরুণের মা সেলাই থামিয়ে মুখ তুলে বললেন, ‘মানে?’
‘হ্যাঁ, তোমাদের বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। ওর কপালে একটা দাগ ছিল। আসলে একটা ক্ষত বা আঁচড়ের মতই মনে হচ্ছিল, ওটার রং ছিল লাল। সুঁই বা কোন পিনের গুঁতো খেয়েছে যেন কেবলই।’
হঠাৎ ভদ্রমহিলা জোরে চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। তাঁর চোখ দিয়ে অনবরত জল গড়াচ্ছে। ‘ওহ্, অ্যানি,’ বলে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। তারপর স্বামী ও ছেলেদের একটা গল্প বললেন, যা নয় বছর তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন।
‘তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন সকালে এটা হয়,’ চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললেন বুড়ো মহিলাটি, ‘বাক্সের মধ্যে শুইয়ে রাখা হয়েছে অ্যানিকে। কামরায় আমি একাই আছি। এতটাই সুন্দর লাগছিল, মনে হচ্ছিল এখনই মা বলে ডেকে উঠবে।’
এক মুহূর্ত কান্না বন্ধ করার জন্য অপেক্ষা করলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন, ‘কিন্তু ওর চুল…সবসময় যখন চুল চূড়া করে বেঁধে রাখত দারুণ লাগত ওকে। আর এটাই ছিল আমার পছন্দ। চাচ্ছিলাম ওভাবেই সুন্দরভাবে কবরে যাক। অ্যানির চুলগুলো পিন দিয়ে সেভাবে আটকে দিতে চাইলাম। কিন্তু…হাতটা প্ৰচণ্ড কাঁপছিল। এসময় ওর কপালে ওটা দিয়ে খোঁচা দিয়ে ফেলি।’ চোখদুটো হাত দিয়ে ঢেকে ফেললেন ভদ্রমহিলা কাঁদতে কাঁদতে। ‘ওর সুন্দর মুখটাতে খুঁত তৈরি করে দিলাম আমি। তবে কেউ দেখতে পায়নি। পাউডার আর মেকআপ দিয়ে ওটা তাড়াতাড়ি ঢেকে দিই,’ বললেন তিনি। ‘কিন্তু অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পুরো সময়টা ঘটনাটা আমাকে যন্ত্রণা দিয়েছে। গত নয় বছরে বারবারই কথাটা মনে হয়েছে আমার। না দেখলে কোনভাবেই এই দাগের কথা বলতে পারতে না তুমি। সত্যি ভাইয়ের কাছে এসেছিল সে। ওহ্, আমার অ্যানি!’
তরুণ হাত দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল। তাঁর পাকা চুলে হাত বুলিয়ে দিল। তার জ্যাকেটের কলারে চোখ মুছলেন মহিলা। ‘ঠিক আছে,’ মার কাঁধের ওপর দিয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে বলল সে, ‘সব ঠিক আছে, মা। সে সুখে আছে। তার চোখ খুশিতে ঝিকমিক করতে দেখেছি। ওপারে ও সত্যি ভাল আছে।’
কয়েক হপ্তা পর তরুণের মা মারা গেলেন। শেষ কয়েকটা দিন ভাল ছিলেন না মোটেই। মেয়ের কথাই বলতেন শুধু। আর চোখের জল ফেলতেন। বোনকে দেখার অভিজ্ঞতাটা বর্ণনা করার আগে যদি মারা যেতেন তবে মেয়ের কপালে আঁচড়ের ঘটনাটা নিজের সঙ্গে কবরে নিয়ে যেতেন তিনি। পৃথিবীর কেউই বলতে পারত না কেন তরুণ ওই দাগটা দেখেছিল।
কিন্তু যখন ভদ্রমহিলা গোপন তথ্যটা ফাঁস করেন তখন এমনকী তাঁর অবিশ্বাসী স্বামীও মেনে নেন মেয়ের ভূত হাজির হয়েছিল ভাইয়ের সামনে। সেন্ট যোসেফের ওই হোটেল রুমে তরুণ কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও বোনের আত্মার মুখোমুখি হয় সেদিন।
আমেরিকান রিসার্চ ফর সাইকিক রিসার্চের ১৮৮৭ সালের সংখ্যায় এ ঘটনাটির বর্ণনা আছে। তাদের ফাইলে আত্মীয়ের প্রেতাত্মার দেখা পাওয়ার অনেক অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ আছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ঘটনাটাকে স্বপ্ন কিংবা হ্যালুসিনেশন হিসাবে ধরে নেয়া হয়। কিন্তু যখন বোনকে দেখে তখন ওই লাল ক্ষতের বিষয়টা তরুণের জানা না থাকায়, এই ঘটনাটা অন্যগুলোর থেকে অতিপ্রাকৃত-বিশেষজ্ঞদের কাছে আলাদা হয়ে রয়েছে।
লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু
উঁচু পাহাড়টার এক পাশে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড গুম্ফাটা। অবস্থানগত কারণে খুব কম পর্যটকই এটা দেখেছে। এমনকী স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে এর সম্পর্কে যেসব ভীতিকর গল্প ছড়িয়ে আছে তা সম্পর্কেও জানে না। যে পর্বতের গায়ে মনাস্ট্রিটা ঝুলে আছে সেটা সাগরসমতল থেকে প্রায় দুই মাইল উঁচুতে। চারপাশে উঁচু সব পর্বতচূড়া গুম্ফাটাকে আড়ালে রাখতে সাহায্য করেছে।
বরফঢাকা হিমালয় ঘেরা বিশাল এক মালভূমি তিব্বত। রহস্যময় এক দেশ এটি। পুরানো রীতি-নীতি নিয়ে টিকে আছে এখনও এর অনেক প্রাচীন মনাস্ট্রি। পর্যটকদের জন্যও অনেকটাই নিষিদ্ধ এলাকা। বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবে এর অনেক কিছুই বদলে গেলেও কোথাও কোথাও নানা ধরনের অদ্ভুত রীতি-নীতি পালন করা হয়।
আমরা এখন যে গুম্ফাটার বর্ণনা দিচ্ছি সেটা কিন্তু এখনও প্রাচীন তিব্বতের বিচিত্র রীতি-নীতি লালন করে আসছে। এর প্রধান লামা খুব ক্ষমতাধর। বলা হয় অদ্ভুত সব ক্ষমতা আছে তাঁর। নানান ধরনের জাদুর রাজা বলা যায় তাঁকে। বিশাল এক দুর্গসদৃশ দালানে বাস করেন তিনি। সেখানে কেবল নির্দিষ্ট কিছু মানুষেরই যাওয়ার সুযোগ মেলে। চারপাশ ঘিরে আছে উঁচু দেয়ালে। এর গায়ে ডজনখানেক জানালা। নিচের ভবনগুলোতে মনাস্ট্রির অন্য লামাদের বাস। উপাসনা আর ধ্যান করে তাঁদের সময় কাটে। আবার আশপাশের গ্রামগুলো থেকে লোকেদের নিয়ে আসা অর্থ-কড়িও সংগ্রহ করেন তাঁরা, গুম্ফার দেখভালের জন্য।
প্রধান লামার দুর্গসদৃশ দালানেই ইয়ামার মন্দির। এখানে বিশাল আকারের একটা কাঠের ভাস্কর্য আছে অন্ধকারের দেবতা ইয়ামার। এর চারপাশ ঘিরে আছে ছোট ছোট কম গুরুত্বপূর্ণ সব ভাস্কর্য। এখনও পুরানো তুকতাক আর মন্ত্রে বিশ্বাসীদের কাছে এই স্ট্যাচু অতি গুরুত্বপূর্ণ। তবে তাদের জানা নেই এর মুখ থেকে যে শব্দ বের হয় তা আসলে কাঠামোটার পেছনে গুপ্ত কামরায় থাকা এক ভিক্ষুর।
এই মন্দিরের লামারা মাথায় এক ধরনের কালো টুপি পরে থাকে। মন্দিরের নিচে গুপ্ত কক্ষে রাশি রাশি স্বর্ণ আর হীরা-জহরত নাকি লুকানো আছে। তবে এই গুল্ফার বুড়ো, কঠিন চোখের লামা ছাড়া আর কেউ জানেন না এর সত্যতা কতটা কিংবা কীভাবে ওই ধনসম্পদের কাছে যাওয়া যায়।
জাপানের কিয়োটোর এক কিউরিও দোকান। একজন ক্রেতাকে হাতে ধরে রাখা খুলির একটা বল সম্পর্কে বলছে বিক্রেতা। ‘স্যর, এটা তিব্বতের খাঁটি জিনিস। এর জন্য আমাকে কেবল আড়াইশো ইয়েন দিতে হবে তোমাকে। এক মানুষের খুলি দিয়ে এটা তৈরি। যে স্থানীয় লোকটার কাছ থেকে আমার এজেন্ট এটা কিনেছে সে বলেছে এটা লাসার দক্ষিণের এক মন্দির থেকে আনা হয়েছে।’
ক্রেতা আর. এল. রিচার্ডসনের জিনিসটা ভারী পছন্দ হয়েছে। এই অদ্ভুত গুম্ফার কথা এই প্রথম শুনছে সে। জিনিসটা কেনার সঙ্গে সঙ্গে ওই মন্দির এবং এর গুপ্তচর্চা সম্পর্কেও যতটা সম্ভব জেনে নিল।
কোন একটা বিষয়ে আগ্রহী হয়ে উঠলে বসে থাকার লোক নয় রিচার্ডসন। লাসার কাছের রহস্যময় ওই মন্দিরের গুপ্তভাণ্ডারের খোঁজে নিজেই যাওয়া স্থির করল। বন্ধুরা তাকে এই কাজ করতে নিষেধ করল বারবার। তবে অভিযান আর পরানো রত্নের গন্ধ যখন পেয়েছে কে ঠেকায় রিচার্ডসনকে!
মে গেল দার্জিলিং। তারপর পাহাড়ি পথে রওয়ানা হলো। সঙ্গে মালপত্র বোঝাই ঘোড়া আর ভয়াল দর্শন কয়েকজন তিব্বতী গাইড। এদের একজনই কেবল ইংরেজি জানে।
পাঁচ সপ্তাহ পাহাড়ি পথে পাড়ি দিয়ে এক সন্ধ্যায় ওই গুম্ফার ধূসর দালানগুলো যে পাহাড়ের কাঁধে অবস্থিত সেখানে পৌছল।
‘এটাই সে জায়গা,’ অল্পবিস্তর ইংরেজি জানা গাইডটি জানাল, ‘এটা কোথায় জানতাম না। তবে অনেক লোককে জিজ্ঞেস করেছি। তারা কেউ বলেছে এখানে, কেউ ওখানে। তবে আমি এটা বের করেছি। বুদ্ধির জোরে। বাড়তি টাকা পাওনা আমার। দিয়ে দাও। কারণ বড় লামা সাদা মানুষ পছন্দ করেন না। বেঁচে ফিরতে পারবে বলে মনে হয় না। সবচেয়ে ভাল হয় যদি ফিরে যাও।’
তবে দুঃসাহসী অভিযাত্রীর পরিকল্পনা ভিন্ন। মালামাল বোঝাই ঘোড়াগুলোকে দাঁড় করিয়ে মনাস্ট্রির পাঁচ মাইল দূরে নিচু এক পাহাড়সারির পেছনে ক্যাম্প করল। তার লোকদের আপাতত এখানেই অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে একাকী রওয়ানা হলো মনাস্ট্রির উদ্দেশে।
আঁকাবাঁকা পাহাড়টার নিচে যখন পৌঁছল তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। দেয়ালের চারকোনা জানালাগুলো গলে কিছুটা আলোর আভাস পাওয়া যাচ্ছে। প্রায় খাড়া দেয়াল বেয়ে উঠতে লাগল রিচার্ডসন। কখনও তার পক্ষে এটা সম্ভব হত না, যদি না ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থাকত।
প্রথম দালানগুলোর কাছে পৌঁছে সাবধানে ভিক্ষুদের বাড়িগুলোকে পাশ কাটিয়ে ওপরের দিকে উঠতে লাগল। পাথরের খাড়া ধাপ ছাড়া ওখানে ওঠার আর কোন উপায় নেই। সন্ধ্যার শীতল বাতাস তার কানে নিয়ে এল একটা ঘণ্টাধ্বনি। ওপরের মন্দির থেকে আসছে।
হঠাৎ কাছের দেয়াল থেকে আলাদা হলো কালো একটা ছায়া। তাড়াতাড়ি রিভলভার বের করে যে কোন পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত হলো রিচার্ডসন। আলখেল্লা পরিহিত এক লামার ছায়া ওটা। মাথায় উঁচু ব্রিমের একটা কালো টুপি শোভা পাচ্ছে। ওটার চূড়াটা বিশেষ আকৃতির এক স্তম্ভের আদলে গড়া।
সিঁড়ি বেয়ে একটা ভূতের মত নেমে গেল ছায়াটা। তার আলখেল্লা রিচার্ডসনের রিভলভার ছুঁয়ে গেল। ভিক্ষু বেশ দূরে চলে গেছে নিশ্চিত হওয়ার পর আবার প্রাচীন সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল রিচার্ডসন। শেষ পর্যন্ত বিশাল আটকোনা দালানটার সদর দরজার সামনে হাজির হলো। এর ভেতরেই তিন মাথার ইয়ামার অবস্থান। প্রধান লামার কামরায় একটা বাতি জ্বলছে। ওটার আলো ছিটকে আসছে উঠনে।
মন্দিরের দরজাটা তালা তো মারা নয়ই, এমনকী বন্ধও না। ছায়ার মত ভেতরে প্রবেশ করল রিচার্ডসন। তারপর বাসি ছাতা পড়া গন্ধের একটা বড় চেম্বারের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ছাদ থেকে ঝুলছে তিব্বতী পর্দা আর নানা ধরনের পেনডেন্ট। বাতাস ভারী। এখানে-সেখানে বাতিদানিতে লাল কয়লা জ্বলছে। পায়ের নিচের মেঝে ঠাণ্ডা, সেঁতসেঁতে। চারপাশে বড় বড় পিলার মাথা উঁচু করে। ওগুলোর গায়ে সময়ের আবর্তে ফিকে হয়ে যাওয়া নানান কারুকাজ। এসব কিছুই ‘রিচার্ডসন দেখছে তার পকেট থেকে বের করা ফ্ল্যাশ লাইটটার আলোয়। একবার এক জায়গায় আরেকবার অন্য জায়গায় আলো ফেলছে। জানে মৃত্যুকে নিজের হাতে তুলে নিয়েছে সে’। তবে বিপদ ভালই লাগে এই প্রাক্তন সৈনিকের। আজকের সন্ধ্যাটা রোমাঞ্চকর কিছু আবিষ্কারের প্রত্যাশা এনে দিয়েছে তার মনে।
সামনেই আরেকটা দরজা। প্রথমটা থেকে ছোট। ভেতরের একটা কক্ষ বা চেম্বারের দিকে গিয়েছে। ওই দ্বিতীয় দরজাটা আগলে থাকা দেবতা আর শয়তানের নানান প্রতিমূর্তি আঁকা পর্দাটার কাছে পৌঁছনোর জন্য বইয়ের বাক্স এবং আরও বিভিন্ন জিনিসের মধ্য দিয়ে এগুল।
পর্দাটা একপাশে সরিয়ে কামরাটার ভেতরে তাকাল। মাটির মেঝের মাঝখানে বড় একটা বাতিদানে রাখা বিশাল একটা মোমের আলোয় আবছাভাবে আলোকিত কামরাটা। দেয়ালে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের ছবি আঁকা। মেঝে ঢাকা পুরানো মোটা কাপড় দিয়ে।
বড় একটা পাত্রে ধূপ জ্বলছে সামনে। এর উল্টোপাশে সোনালি গিল্টি করা একটা দরজা পেরোলেই গুপ্তকুঠুরী। দরজা গলে ঝিকমিক করতে থাকা মন্দিরটার দিকে চোখ গেল ‘তার। কাঁপতে থাকা মোমের আলোয় শত শত ছায়া দেখা যাচ্ছে। এদিকে চেম্বারগুলোর ভেতর দিয়ে বয়ে চলা বাতাস অদ্ভুত একটা হিস হিস শব্দ তৈরি করছে। চারপাশ ধূপের ধোঁয়ায় কেমন ছায়া ছায়া হয়ে আছে। সব জায়গায় কেমন আলো-আঁধারির খেলা।
কেঁপে উঠল রিচার্ডসন। তারপরও রিভলভারটা আঁকড়ে ধরে গেট পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল। চারপাশে ছোট ছোট দেবতাদের ঘেরাওয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বিকট দর্শন ইয়ামা। তার তিন মুখে বীভৎস ভঙ্গি। বুকে ক্রুশ আঁকল রিচার্ডসন। পরমুহূর্তেই হাসি ছড়িয়ে পড়ল সারা মুখে। ধর্মীয় অমূল্য সব কিউরিওতে পরিপূর্ণ গোটা কামরাটা। পান্না, রুবিতে মোড়া খুলির বাটি, মূল্যবান সব পাথরের জপমালা, অসাধারণ কারুকার্যমণ্ডিত ঝুলতে থাকা কাপড়, মূল্যবান পাথর ঝকমক করতে থাকা ছোট মূর্তি, দামি চিত্রকর্ম-এসব কিছু দেখে রিচার্ডসনের তো দিশেহারা অবস্থা। তবে মাথা ঠাণ্ডা রাখল। মূল্যবান আর ছোট জিনিসগুলোই সে হাতিয়ে নেবে।
পান্নার চোখ এবং কপালে হীরে আটকানো জেড পাথরের ছোট্ট এক বুদ্ধমূর্তি তার মনে ধরল। ওটা পকেটে চালান করল। এবার সোনার গিল্টি করা ইয়ামার দিকে তাকাল। দামি সব মুক্তো দিয়ে তৈরি একটা হার ঝুলছে তার গলায়। কীভাবে ওখানে পৌছানো যায় বুঝতে চারপাশে তাকাল। একটা ছোট সিঁড়ি নজর কাড়ল।
ওটা ধরে উঠতেই বহু হাতের ওই দেবতার পেছনে নিজেকে আবিষ্কার করল। আর তখনই বুঝতে পারল ওটা ফাঁপা। মূর্তিটার শূন্য কোটর দিয়ে অনায়াসে তাকাতে পারল রিচার্ডসন।
মুখটা ভেতর থেকে খোদাই করা। তবে তার জানা নেই এখন যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে কখনও এসে দাঁড়ান প্রধান লামা। ছোট্ট ছুরির এক খোঁচায় কাঠের পেরেকদুটো খুলে ফেলতেই মুক্তোগুলো এসে হাতে জমা হলো।
মন্দিরের সামনে ফিরে এসে রত্নখচিত জপমালাটা হস্তগত করে সিদ্ধান্তে পৌঁছল যথেষ্ট হয়েছে। আরও অনেক কিছুই তার পছন্দ। তবে বুদ্ধিমান রিচার্ডসন জানে এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাণ নিয়ে ফেরা।
গিল্টি করা দরজা ঠেলে বের হয়ে আবারও সেই শত ছায়ার রুমে প্রবেশ করল। কামরাটার আশ্চর্য নীরবতা তাকে আঁকড়ে ধরল। ভয় পেয়ে গেল কেন যেন। হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে লাগল। ব্রোঞ্জের বাতিদানের মধ্যে বিশাল মোমবাতিটাকে পাশ কাটাল। অশুভ জায়গাটি ছেড়ে চলে যেতে ইচ্ছা করলেও থেমে চারপাশে দৃষ্টি বোলাল। মৃদু, ব্যাখ্যাতীত একটা শব্দ কানে এল তার। আবছা আলো- আঁধারিতে প্রতিটি কোণ এবং কুলুঙ্গিতে খেলা করা ছায়াগুলো দেখে চুলগুলো খাড়া হয়ে গেল।
হঠাৎই বুঝতে পারল ছায়াগুলো জীবন্ত। মনে মনে নিজেকে একটা ধমক দিল। এটা অবশ্যই কল্পনা। আবার তাকাল। এবার আর কোন ভুল নেই। চওড়া কিনারার একটা কালো টুপি নজর কাড়ল তার। ধীরে ধীরে এদিকেই এগিয়ে আসছে। যে দরজাটা কেবল পেরিয়ে এসেছে সেদিকে তাকাল। আতঙ্কে পিছু হটল। আরেকটা ছায়ামূর্তি দেখা যাচ্ছে। ওটার মাথায়ও কালো টুপি। যেদিকেই তাকাল কালো টুপির ছায়ামূর্তি দেখতে পেল। পালাবার পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে তার। দ্রুত ঘুরে ভেতরের মন্দিরের দিকে যাওয়া দরজাটার দিকে এগুল। ওটা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে দরজা আটকে দিল। সে নিশ্চিত এই কামরাতে ঢুকবার কিংবা এর থেকে বেরোবার আর কোন পথ নেই। চারপাশের ছায়াগুলো দেখছে।
হঠাৎ একটা আলোর ঝলকানি। এটা কোন দৃষ্টিবিভ্রম নয়। ভুতুড়ে এক কাঠামো, যেটাকে ছায়া ভেবেছিল, ওটার হাতে শোভা পাচ্ছে ধারালো এক ছুরি। শিস দেয়ার মত একটা আওয়াজ। প্রবৃত্তিগতভাবে মাথা নিচু করল রিচার্ডসন। আর এটাই জীবন বাঁচিয়ে দিল তার। যেখানে মুখটা ছিল সে জায়গাটা দিয়ে সজোরে চলে গেল পাতলা একটা ইস্পাতের ছুরি। ব্রোঞ্জের একটা বলে বাড়ি খেয়ে তার পায়ের ওপর পড়ল ওটা।
ছায়াগুলোর মধ্যে একটাকে লক্ষ্য করে পিস্তল তাক করল রিচার্ডসন। তারপর আরেকটাকে নিশানা করল। কিন্তু বুঝতে পারল কোন লাভ হবে না। ওগুলো খুব ঝাপসা। পকেট থেকে টর্চটা বের করে একটা অন্ধকার কোণ লক্ষ্য করে বাতিটা জ্বালল। আঁধার কেটে যাওয়া আলোকরশ্মিতে লম্বা, পাতলা একটা কাঠামো ধরা দিল। গায়ে এক জাতের হরিণের চামড়ার পোশাক, মাথায় কালো টুপি। আলো পড়তেই দেয়ালের গায়ে ঝুলতে থাকা নকশাখচিত কাপড়ের ওপাশে হারিয়ে গেল কাঠামোটা। তারপরই একটা চিৎকার শোনা গেল। নানা দিক থেকে ছুরি হাতে ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসতে লাগল।
রিচার্ডসনের হাতের রিভলভার আগুন ঝরাল। চিৎকারের সঙ্গে যোগ হলো গোঙানি। দুটো কাঠামো মাটিতে আছড়ে পড়ল। পরমুহূর্তে খালি হয়ে গেল কামরাটা।
একটার পর একটা ঘণ্টা পেরিয়ে যেতে লাগল। রিচার্ডসন কড়া পাহারায় আছে। কিছুই এল না। এখান থেকে নড়তে সাহস করল না সে। দরজাটা কয়েক ইঞ্চি ফাঁক করতেই মৃদু একটা আওয়াজ শুনল। সেদিকে টর্চের আলো ফেলল। দেখল দেয়ালের পর্দাগুলো একটু নড়ছে।
ভোর হলো। একই সঙ্গে ক্লান্ত, চিন্তিত রিচার্ডসনের দিশেহারা অবস্থা। একটা সেগুন কাঠের টুলের ওপর বসল। সূর্যের আলো ভেতরে ঢুকতে পারছে কমই। কেবল আবছা একটা আলোর আভা জানিয়ে দিল ভোরের আগমনী। কামরাটা বিশেষ করে যে ছোট্ট চেম্বারটায় আছে সেটা ভালভাবে পরীক্ষা করতে লাগল।
ঈষৎ দুলতে থাকা পর্দা ভরা এই হল ছাড়া পালানোর আর কোন রাস্তা যে সামনে খোলা নেই এটা ভালই বুঝতে পারছে রিচার্ডসন। এটা করার চেষ্টা করলে অন্তত বিশটা ছুরি তার পিঠে গাঁথবে। মাটিতে ভূপাতিত দুই লামার দেহ অদৃশ্য হয়েছে। কে তাদের নিয়েছে বলতে পারবে না।
দরজার গরাদের ফাঁক দিয়ে যখন দেয়াল এবং ছাদ পর্যবেক্ষণ করছে হঠাৎ বুঝতে পারল, পায়ের নিচে মাটি নড়ছে তার। পাথুরে ভূমি যেন একটু একটু করে ওপরে উঠছে।
লাফিয়ে সরে গিয়ে তাকাল লুকানোর একটা জায়গার খোঁজে। এসময়ই বুদ্ধিটা এল মাথায়। ইয়ামার ফাঁপা শরীরটার ভেতরেই তো লুকাতে পারে সে।
গিল্ড করা দরজার ওপর দ্রুত একটা পর্দা ফেলল, যেন তার গতিবিধি কারও নজরে না পড়ে। ভুতুড়ে দেবতার কাঠামোর দিকে সিঁড়ি ধরে এগিয়ে গেল। তারপর বিশাল মূর্তিটার পেছনে ঢুকে পড়ল অনায়াসে।
ইয়ামার শূন্যগর্ভ চোখ দিয়ে দেখছে সে। মাটি আস্তে আস্তে ওপরে উঠেই চলেছে। মাটির সমতলের কয়েক ইঞ্চি নিচে একটা ট্র্যাপডোর আছে নিশ্চিতভাবেই। সম্ভবত মন্দিরের নিচের মূল্যবান হীরা-জহরতের ভল্টের দিকে গিয়েছে ওটা।
একটু একটু করে ওপরে উঠছে মেঝের ওই অংশ। ট্র্যাপডোরের ওপরের অংশটা ধরে থাকা লম্বা হলুদ একটা হাত নজরে পড়ল। কয়েক সেকেণ্ড পর কালো টুপি পরা একটা কাঠামো খোলা অংশটা দিয়ে চেহারা দেখাল। সিঁড়ি ধরে এসে বিশাল স্ট্যাচুর সামনে দাঁড়াল লামা।
তারপর একজনের পর একজন আসতেই লাগল। এভাবে জনা বারো লামা হাজির হলো গুপ্ত দরজাটা দিয়ে। রিচার্ডসন টু শব্দটি করছে না। লামারা খোঁজ করতে লাগল তার। দরজা খুলে দেখল। ভেতর থেকে যোগ দিল আরও কয়েকজন। উত্তেজিতভাবে কথা বলতে বলতে কামরার নানা দিকে নির্দেশ করছে। তবে ইয়ামার স্ট্যাচুর দিকে নজর নেই কারও। তারপরই একজনের নজরে পড়ল দেবতার হার গায়েব। অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ক্রোধে, দুঃখে চেঁচিয়ে উঠল সবাই।
এসময়ই প্রধান লামা বা মন্দিরের অধ্যক্ষ হাজির হলেন। গলায় পেঁচানো নানা ধরনের মূল্যবান পাথরের অনেকগুলো জপমালা। নিচু স্বরে কী যেন বললেন। সঙ্গে সঙ্গে চারজন লামা সিঁড়ি বেয়ে ইয়ামার ভাস্কর্যের দিকে আসতে লাগল। নেকলেসটা চুরি করায় নিজেকে অভিশাপ দিল রিচার্ডসন তবে এখন আর অতীতের ভুলের কথা ভেবে লাভ নেই। প্রথম লামাটির মাথা নজরে আসতেই ঘুরে গুলি করল। একটা চিৎকার। পরক্ষণেই ভিক্ষুরা সঙ্গীর দেহটা নিয়ে পিছু হটল। সবাই গিল্টি করা দেবতার মূর্তির পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে থাকল কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে।
প্রধান লামা কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন। তারপর নিচু কণ্ঠে বেশ কিছুটা সময় ধরে নির্দেশ দিলেন। সবাই ছোটাছুটি শুরু করল। এক ঘণ্টা পর তিনজন ফিরল। দু’জন ভারী একটা টেবিল বহন করে এনেছে। ওটাকে মেঝেতে পাতা হলো। লম্বা একটা বোর্ডের ভারে রীতিমত নুয়ে পড়েছে আরেকজন। ওটার ওপরে ময়দা দিয়ে বানানো মানুষের একটা কাঠামো শোয়ানো। এখানে নরবলি দেয়া নিষিদ্ধ। এর বদলে ময়দায় তৈরি মানুষের কাঠামো ব্যবহার করা হয়। একজন সাদা মানুষকে চিহ্নিত করা হয়েছে এখানে। এবার ওটাকে টেবিলের ওপর রেখে তিনজন অদৃশ্য হলো।
একটার পর একটা ঘণ্টা পেরোতে লাগল। আবারও সন্ধ্যা এল। একজন লামার নিয়ে আসা মোম আবছা আলো ছড়াচ্ছে ময়দার কাঠামোটার ওপর। কেউ নেই দেখে ফাটল দিয়ে বেরিয়ে এল রিচার্ডসন, হাত-পায়ের খিল ছাড়ানোর জন্য। আরও একটা রাতের আতঙ্ক চেপে ধরল তাকে। খাবার, পানি ছাড়া এভাবে কয়দিন বাঁচতে পারবে জানে না। তবে পৃথিবীর মায়া এখনই কাটাতে চায় না।
ঘড়িতে যখন দশটা তখন আবার ছায়াময় কিছু কাঠামো একটার পর একটা হাজির হতে লাগল। জমকালো পোশাক পরনে। অনেকের মাথায় সিংহ, পাখি, ড্রাগন নানান কিছুর মুখোশ। কাঁপছে, মন্ত্র পড়ছে ছায়ামূর্তিগুলো। ওগুলো কি মানুষ নাকি অন্য কিছু বলতে পারবে না রিচার্ডসন। হঠাৎ অদ্ভুত জিনিসগুলোর মাঝখানে আবির্ভূত হলেন প্রধান লামা। ঢিলেঢালা জমকালো এক আলখেল্লা পরনে, মাথায় কালো টুপি। এক হাতে একটা মশালের মত, অন্যহাতে লম্বা একটা লাঠির মাথায় সুচালো ইস্পাতের ফলা। ইয়ামার দিকে মুখ উঁচু করে কথা বলতে শুরু করলেন, ‘সাদা মানুষ, তুমি আমাদের পবিত্র মন্দির লুঠ করতে এসেছ। ইয়ামার হার চুরি করেছ। আমরা তোমাকে আঘাত করিনি। কিন্তু তুমি আমাদের ভিক্ষুদের হত্যা করেছ। এখন দুটো পথ খোলা আছে তোমার সামনে। শয়তানি লাঠিটা (রিভলভার) ব্যবহার করে মরো, নতুবা আমরা তোমাকে মারব। তুমি পালাতে পারবে না। আমাদের এক ডজনকে মারলেও বাকিরা তোমাকে হত্যা করবে। আমরা চাইলে অনাহারে রেখেও মারতে পারি তোমাকে। এর চেয়ে নিজে নিজেই মরো।’
নিঃশব্দে হাসল রিচার্ডসন। মূর্তির অশুভ হাঁ করা মুখটার মাঝখান দিয়ে নিশানা করে গুলি করল। বুড়ো লামার শরীরটা কেঁপে উঠল। হাত থেকে মশালের মত জিনিসটা খসে পড়ল। তাঁর কাঁধ ভেদ করে গিয়েছে বুলেট। দু’জন লামা তাঁকে সাহায্য করতে এগুল। কিন্তু হাত নেড়ে নিষেধ করলেন। মন্দিরের ওই অদ্ভুত মানুষ কিংবা জন্তুগুলোকে সঙ্গে নিয়ে এগুলেন তিনি। ময়দার তাল দিয়ে তৈরি কাঠামোটার সামনে দাঁড়ালেন। একজন সহকারী একটা ধারালো ছুরি এনে দিল তাঁকে।
ইয়ামার মুখের দিকে চোখ তুলে মন্ত্র আওড়াতে শুরু করলেন প্রধান লামা। ক্রমেই বাড়তে লাগল তাঁর কণ্ঠের জোর। সেই সঙ্গে বেজে উঠল মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি। চারপাশে ঘিরে থাকা অদ্ভুত ওই ছায়ামূর্তিগুলো পৈশাচিক কণ্ঠে হুল্লোড় করছে।
রিচার্ডসনের কেমন ঘুম ঘুম আসছে। খাবার আর ঘুমের অভাবেই এমনটা হয়েছে, ভাবল সে।
কান ফাটানো একটা অশুভ চিৎকারের মধ্য দিয়ে শেষ হলো প্রধান লামার মন্ত্রপাঠ। যেন মৃত্যুপথযাত্রী কোন ঈগলের মরণ চিৎকার। তারপর আশ্চর্য নীরবতা। মাথা তুলে লুকিয়ে থাকা সাদা মানুষের উদ্দেশে বললেন, ‘তুমি নিজের মৃত্যু নিশ্চিত করোনি। এবার লামাদের জাদুর হাতে মরবে। কিছুই করতে পারবে না। কারণ লামাদের গুপ্ত জ্ঞান সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই তোমাদের সাদা মানুষদের।’
ঝুঁকে পড়ে ছুরিটা দিয়ে ময়দার মূর্তিটার এক হাত কেটে ফেললেন তিনি। ওটা মাটিতে ছুঁড়ে মারলেন। ওখান থেকে রক্তের মত একটা কিছু বেরোতে লাগল।
ইয়ামার ভেতর থেকে অমানুষিক এক আর্তনাদ শোনা গেল। এবার অপর হাতটা কাটলেন লামা। তারপর দুই পা। ভয়ঙ্কর এক আঘাতে ময়দার তালটাকে রীতিমত ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে পারলেন।
সবশেষে মাথাটা বিচ্ছিন্ন করলেন। এটা যখন করলেন ভেতরের গোঙানি থেমে গেল। তারপরই কাঠের কাঠামোটা বেদি থেকে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল। ওটার ওপর পড়ে বেদিটাকেই খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলল। তারপর পড়ল টেবিলের ওপর। টেবিলটাকে ভেঙে ফাঁপা কাঠামোটা অন্তত এক ডজন টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে। প্রধান লামার কাঁপতে থাকা শরীরটা, যেটা অন্য লামারা ধরে রেখেছে, রিচার্ডসনের কাঠামোটার দিকে তাকাল। ময়দার তালটা যেভাবে কাটা হয়েছে সেভাবেই কাটা পড়েছে সাদা মানুষের শরীরটা।
অভিশপ্ত অরণ্য হইয়া বাচিয়ু
রোমানিয়ার ক্লাজ-নেপোকার কাছে ছোট্ট এক বন হইয়া বাচিয়ু। আয়তন মোটে ২৫০ হেক্টর। কিন্তু আকারে ছোট হলে কী হবে নানা ধরনের অতিপ্রাকৃত ও ব্যাখ্যাতীত ঘটনার জন্য এ বনকে চেনে সবাই এক নামে। রোমানিয়ার বারমুডা ট্রায়াঙ্গলও বলেন কেউ কেউ। ভুতুড়ে ছায়ামূর্তি, খালি চোখে দেখা যায়নি এমন সব ছবি ক্যামেরায় আসা, এমনকী ভিনগ্রহের যান বা উড়ন্ত সসার নামার কাহিনীও ডালপালা বিস্তার করেছে এই অরণ্যকে ঘিরে। জঙ্গলটার বয়সও কম নয়, পঞ্চান্ন হাজার বছর। এটা যে অঞ্চলে অবস্থিত সেই ক্লাজ-নেপোকা আবার ঐতিহাসিকভাবে কাউন্ট ড্রাকুলার বাসস্থান হিসাবে পরিচিত ট্রানসিলভানিয়ার অংশ। তাই হইয়া বাচিয়ু পরিচিতি পেয়েছে আরও বেশি।
এই বনে ঘুরে বেড়ানো পর্যটকদের হঠাৎ অস্বস্তি হতে শুরু করে। কেউ আবার বলে, অদৃশ্য কিছু তার দিকে নজর রাখছে। যদিও কাউকে দেখা যায় না। এখানকার গাছপালাগুলোও কেমন অদ্ভুত।
এক মেষপালক দুইশো ভেড়াসহ অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার পরই জঙ্গলটা অভিশপ্ত হিসাবে কুখ্যাতি অর্জন করে আশপাশের এলাকাগুলোয়। ছেলেটাকে ভেড়ার পাল নিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেখে অনেকেই। তবে আর ফিরে আসেনি কখনও। অরণ্যটির কাছাকাছি বাস করা লোকজন এর ভেতরে ঢুকতে ভয় পায়। তাদের ধারণা এই জঙ্গলে একবার যে ঢোকে তার ফিরে আসার গ্যারান্টি নেই। সাহসী কিছু মানুষ অবশ্য ভিতরে ঢোকে কখনও-সখনও। তবে তাদের নানা ধরনের সমস্যা তৈরি হয়। যেমন শরীরে র্যাশ ওঠা, বিষাদভাব, বমি, আঁচড়, দুশ্চিন্তাসহ বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক সমস্যা।
১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে ভুতুড়ে এই জঙ্গল একেবারে অন্য একটি কারণে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করে। এসময় আলেকজাণ্ডার সিফট নামের এক জীববিদ জঙ্গলের ওপরে উড়ন্ত সসার সদৃশ কিছু বস্তুর ছবি তোলেন। ১৯৬৮ সালের ১৮ আগস্ট এমিল বার্নিয়া নামের এক সামরিক প্রকৌশলীও জঙ্গলের ওপর দিয়ে ফ্লাইং সসার উড়ে যাওয়ার এক ছবি তুলে রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে যান। ১৯৭০- এর দশকে আরও অনেকেই এখানে উড়ন্ত সসার দেখার দাবি তোলেন। আবার ব্যাখ্যাতীত সব আলো খেলা করতে দেখা যায় অরণ্যের গভীরে।
ম্যারা এই বনে ঢোকে তাদের বেশিরভাগেরই অসুস্থবোধ হতে থাকে, মাথাটা একেবারে হালকা মনে হয়। কখনও কখনও আবার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এলোমেলো আচরণ করতে থাকে। অতিপ্রাকৃত বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের দাবি অশরীরীর উপস্থিতির কারণেই এমনটা ঘটে। তাঁদের দাবি উড়িয়ে দেয়া কঠিন। কারণ এখানে নানান ধরনের অদ্ভুত কাণ্ড-কারখানার প্রমাণ মিলেছে বিভিন্ন সময়। রহস্যময় আলো দেখার কথা বলে জঙ্গলে ঢোকা প্রায় সবাই-ই। হঠাৎ বনের শান্ত পরিবেশ নষ্ট করে দেয় নারী কণ্ঠের শব্দ, খিলখিল হাসি। হঠাৎ হাজির হয় ছায়ামূর্তি, গায়েব হয়ে যায় আবার। আবার বন থেকে বেরিয়ে আসার পর কেউ কেউ শরীরে আবিষ্কার করে ক্ষতের চিহ্ন। যেন নখ দিয়ে আঁচড় কেটেছে কেউ। পোড়া দাগও পাওয়া যায় কোন কোন পর্যটকের দেহে।
অনেকে আবার মনে করে অন্য জগতে যাওয়ার দরজা এই হইয়া বাচিয়ু। ভেতরে ঢুকে অনেক লোকেরই আর ফিরে না আসার গল্প চালু আছে। কারও কারও মতে সংখ্যাটা এক হাজার ছাড়িয়েছে। হঠাৎ বইতে শুরু করে বাতাস। ভেতরে ঢোকার পর সময় এলোমেলো হয়ে যাওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন কোন কোন অভিযাত্রী। কেউ বেশ কিছুটা সময় কী করেছেন বলতে পারেন না। যেমন পাঁচ বছরের এক স্থানীয় মেয়ে গাছপালার মাঝে হাঁটতে হাঁটতে হারিয়ে যায়। পাঁচ বছর পর ফিরে পাওয়া যায় তাকে। তবে সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার যে পোশাকটা পরা ছিল পাঁচ বছর আগে সেটাই পরনে, এই সময়টা কোথায় ছিল, কী করেছে এ ব্যাপারে মেয়েটার কোন ধারণাই নেই। অবশ্য কোন কোন গল্পে দাবি করা হয় তার গায়ের রংটা বেশ বদলে গিয়েছিল।
এই বন ঘিরে আরেকটি ঘটনা প্রচলিত আছে। একসময় এখানে বেশ কিছু রোমানীয় চাষী খুন হয়। তাদের অতৃপ্ত আত্মারা নাকি এখনও ঘুরে বেড়ায় জঙ্গলে। নিজেদের দুর্দশার জন্য এরা বেশ খেপে থাকে। পর্যটকদের সামনে হঠাৎ হাজির হয়ে তাদের চমকে দেয় এই অশরীরীরা। কখনও শূন্যে ভাসতে দেখা যায় সবুজ চোখ। ভারী কালো কুয়াশায় ঢেকে যায় চারপাশ। বেশিদিন হয়নি টেলিভিশনের জন্য অতিপ্রাকৃত এক কাহিনী বানানোর জন্য ক্যামেরা নিয়ে জঙ্গলের অপেক্ষাকৃত খোলা জায়গায় বসে ছিলেন এক রিপোর্টার। রাতে তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় অদৃশ্য কোন শক্তি। গাছপালার মাঝখানে হঠাৎ জ্বলে ওঠে চোখ ধাঁধানো আলো।
জঙ্গলের মাঝখানে একটা খোলা জায়গা আছে যেখানে কোন গাছপালা জন্মে না, সেখানে ভুতুড়ে ঘটনাগুলো ঘটে সবচেয়ে বেশি। মোটামুটি বৃত্তাকার জায়গাটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে ওখানকার মাটির মধ্যে উদ্ভিদ জন্মানোর জন্য প্রয়োজনীয় কোন কিছুরই ঘাটতি নেই। বলা হয় এই গোল জায়গাটিই ভূতেদের আস্তানা। একটি সূত্রের দাবি, এখানে ঘুরে বেড়ানো প্রেতাত্মারা জায়গাটিকে আগলে রেখেছে। কারণ এটাই অন্য পৃথিবীতে যাওয়ার গুপ্তস্থান। এদিকে এই অরণ্যে তোলা বিভিন্ন ছবিতে পাওয়া গেছে ভাসতে থাকা আকৃতি, রহস্যময় মানুষের কাঠামো।
সন্দেহ নেই মানুষ এ বনের অনেক কাহিনীকেই রং চড়িয়ে বলে। তবে এখানে যে অস্বাভাবিক কোন শক্তির উপস্থিতি আছে তা অস্বীকার করার জো নেই। গভীর জঙ্গলের ভেতর থেকে ভেসে আসতে দেখা যায় অনেকগুলো গোল আলো। তাপ শনাক্তকারী যন্ত্র ব্যবহার করে এই আলোগুলোয় কোন তাপের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি। বনে ঢোকার পর অনেকেরই হারিয়ে যাওয়া পুরানো সব স্মৃতি মনে পড়ে যায়, কিন্তু এই এলাকা ছাড়ার পর আবার হারিয়ে যায় ওই স্মৃতিগুলো।
স্বাভাবিকভাবেই বনটা পৃথিবীর নানা প্রান্তের গবেষকদের আকৃষ্ট করেছে। জার্মানি, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও হাঙ্গেরিসহ অনেক দেশের গবেষকই বহু সময় দিয়েছেন এখানকার রহস্য সমাধানে। কারও কারও তোলা ছবি ওয়াশ করার পর তাতে মিলেছে ভৌতিক মুখ বা কাঠামো। এর কোন কোনটা খালি চোখেও ধরা দিয়েছিল। কোনটা আবার কেবল ছবিতেই দেখা গিয়েছে। বেশিরভাগ অতিপ্রাকৃত বিশেষজ্ঞের ধারণা রোমানিয়ার সবচেয়ে ভৌতিক জায়গা এই মুহুর্তে হইয়া বাচিয়ু। ট্র্যাভেল, অ্যাণ্ড লেইজার ম্যাগাজিন এবং বিবিসির মত বিখ্যাত পত্রিকাও একে পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত ভৌতিক এলাকা ও অরণ্যের তালিকায় রেখেছে। তাই সাহস করে রোমাঞ্চপিয়াসী পর্যটকরাও হানা দিচ্ছে অরণ্যটিতে। কয়েক বছর আগে হলিউড অভিনেতা নিকোলাস কেইজ এক ছবির শুটিং করতে এসেছিলেন রোমানিয়ায়। তখন ক্লাজ-নেপোকায় আসেন রহস্যময় অরণ্যটিকে একবার দেখতে। জঙ্গলটির আরও একটা অদ্ভুত বিষয় অনেকেরই চোখে পড়ে। এখানকার কোন কোন গাছ বাঁকা হয়ে আছে। রহস্যময় কোন অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাবেই নাকি এটা হয়।
শুধু যে ভুতুড়ে কাণ্ড-কারখানার জন্য এলাকাটি বিখ্যাত তা কিন্তু নয়। এ অরণ্যের আশপাশের এলাকায় নানা ধরনের উৎসবও হয়। ক্লাজ-নেপোকা এমনিতেও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের জন্য পর্যটক টানে। এখন অনেক পর্যটকই ভুতুড়ে বনের রাস্তা ধরে সাইকেল চালান, এঁদের কারও কারও টুকটাক সমস্যা হওয়ার খবর পাওয়া গেলেও বেশিরভাগই কিন্তু ফিরে এসেছেন বহাল তবিয়তে। কাজেই একবার চেষ্টা করেই দেখতে পারেন অরণ্যটার রহস্য সমাধানে। উপরি হিসাবে পেতে পারেন ভালুক, হরিণসহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর দেখা।
ভুতুড়ে সিঙ্গাপুর
সিঙ্গাপুরের বেশ কিছু ভৌতিক ঘটনা সত্য হরর কাহিনী সিরিজের আগের বইগুলোতে ছাপা বইগুলোতে ছাপা হয়েছে। ধারাবাহিকতায় ওখানকার বাছাই করা কয়েকটি অতিপ্রাকৃত ঘটনা পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি এই বইটিতেও।
ওমরের গল্প
এবারের কাহিনীটি বলেন একজন বিমান স্টুয়ার্ড। তাঁর নাম কামাল বিন মুস্তফা। আমরা বরং এটা তাঁর জবানীতেই শুনি।
এর নায়ক বা খলনায়ক যা-ই বলি না কেন আমার ভাই ওমর। আমাদের ছোটবেলার কথা। নিউটন সার্কাস এলাকায় বেড়ে উঠেছি। বাড়ির উল্টোপাশে মনক’স স্কুলের ফুটবল মাঠ। অন্য বাচ্চাদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে প্রতিদিন বিকালে সেখানে হাজির হতাম আমরা।
একদিন সন্ধ্যার আগে, ওমর বলটা লাথি মেরে পাঠায় মাঠের কিনারে একটা কুৎসিত দর্শন, অশুভ গাছের দিকে। ওটা আনতে গিয়ে দেখলাম, গাছে বাস করা অশুভ আত্মাদের শান্ত রাখতে যেসব লাল চীনা ফলক ব্যবহার করা হয় এর একটাকে উপড়ে ফেলেছে বলটা।
ওমরকে অবশ্য এটা নিয়ে খুব একটা চিন্তিত মনে হলো না। বেশ সাহসী ছেলে সে। কিন্তু আমরা বাকি ছেলেরা বেশ ভয় পেয়ে গেলাম। ওই ফলকটা ভেঙে লাল টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে গাছের নিচে।
ওখানে যখন আমরা দাঁড়িয়ে আছি তখনই হঠাৎ ঝড়ো বাতাস বইতে শুরু করল। গাছটার ডালপালাগুলো সে হাওয়ায় অদ্ভুত শব্দ তৈরি করল। আকাশ ঢেকে গেছে ঘন কালো মেঘে। যেন বৃষ্টি নামবে। আমরা তাড়াহুড়ো করে যার যার বাড়ির দিকে দৌড়লাম।
রাতে আমাদের সবার ঘুম ভেঙে গেল ওমরের চিৎকারে। ওর পাজোড়া ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছে। কাঁদতে কাঁদতে বলল অনেক কষ্ট হচ্ছে তার।
চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো সকালে। কিন্তু কেন এমনটা হয়েছে বলতে পারলেন না তিনি। উপায়ান্তর না দেখে ইপোহর একজন বোমা বা ওঝার শরণাপন্ন হলাম আমরা।
সাদা চুলের বুড়ো এক মানুষ তিনি। বেশিরভাগ আঙুলে নানা ধরনের পাথর শোভা পাচ্ছে তাঁর। সব কিছু খুলে বলার পর অদ্ভুত গন্ধের একটা মলম লাগানো কলা পাতা দিয়ে ওমরের পাদুটো মুড়ে দিলেন। তারপর দুর্বোধ্য কোন ভাষায় মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে ধূপ পোড়াতে লাগলেন।
আমাদের নিয়ে যে গাছটার নিচে ওই লাল ফলক ছিল সেখানে চলে এলেন ওঝা। বেশ কিছু ফল রেখে দিলেন জায়গাটিতে। এসব আনুষ্ঠানিকতা শেষ হতেই ওঝার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ির পথ ধরলাম আমরা। ওমরের কান্না থেমে গেছে। বলল ওর পা আর যন্ত্রণা করছে না।
কয়েকদিনের মধ্যে পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠল ওমর। আবার প্রতিবেশী বাচ্চাদের সঙ্গে ফুটবল খেলা শুরু করলাম আমরা। তবে তখন খেলার সময় খেয়াল রাখতাম অশুভ ওই গাছটার কাছ থেকে যেন বল দূরে থাকে।
পুরানো স্কুল
এবারের অভিজ্ঞতাটি বেলিন্দা ওয়ং নামের এক মডেলের।
মাউন্ট ফেবার ধরে আমার প্রেমিকের সঙ্গে গাড়িতে করে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ তার সঙ্গে একটা বিষয়ে তুমুল তর্ক শুরু হয়। মেজাজটা এতটাই খিঁচড়ে যায় যে আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিতে বললাম। তখন বেশ রাত। রাস্তাও ফাঁকা কিন্তু সে এতটাই অমানুষ যে আমাকে নেমে যেতে দিল
কিছুক্ষণ হাঁটতেই শীতল বাতাসে গরম মাথাটা আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হলো। বুঝতে পারলাম এখানে এই রাতে নেমে পড়ে বোকামি করেছি। আকাশ চিরে ফালা ফালা করে দিয়ে বিদ্যুতের ঝলকানি দেখা যাচ্ছে। যে কোন সময় বৃষ্টি শুরু হবে। কেমপং সিলাট ধরে হাঁটছি এমন সময় বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেল সত্যি সত্যি। আশপাশে কোন গাড়ি-ঘোড়া নেই। অতএব পুরানো এক স্কুলভবনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলাম।
পুরানো রাডিন মাস স্কুল ওটা। বহু বছর ধরেই এখানে লোকজনের ততটা আনাগোনা নেই। বিশেষ করে স্কুলভবনটা পরিত্যক্ত হবার পর থেকে। তাই এখানে কোন বাতি বা প্রহরী নেই। স্কুলের চারপাশের ছিন্ন বেড়ার ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়তে পারলাম।
গোটা দালানটায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। তবে ঝড়ের জন্য এটা মোটামুটি ভাল আশ্রয়। তাছাড়া আমি বেশ সাহসী, মেয়ে। অন্ধকার করিডোর ধরে হাঁটতে লাগলাম। ভাঙা জানালা গলে যখনই ঝড়ো বাতাস ভেতরে ঢুকছে প্রতিটি আনাচে-কানাচে নানা ধরনের ছায়া খেলা করছে। অব্যবহৃত ক্লাসরুমগুলোর দিকে তাকালাম। ওগুলোর অবস্থা দেখে করুণা হলো। সব টেবিল আর টুল উল্টানো, ভাঙা। দেয়ালে আশ্চর্য সব চিত্র আঁকা। বাস্তব দুনিয়ার কিছুর সঙ্গে এই চিত্রগুলোর মিল আছে কমই। অন্ধকারে আমার পায়ের আওয়াজের প্রতিধ্বনি শুনে বুঝতে পারলাম একাই আছি এখানে। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক। এসময়ই ফিক ফিক হাসির শব্দ শুনলাম। ওপরের সিঁড়িগুলোতে ছোট ছেলে-মেয়েদের দৌড়াদৌড়ির আওয়াজও পেলাম। প্রথমে বেশ স্বস্তি পেলাম। মনে হলো, যাক, কিছু বাচ্চাও মনে হয় কীভাবে যেন এই বৃষ্টিতে এখানেই আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু সিঁড়ি ধরে যেখান থেকে আওয়াজটা আসছে মনে হচ্ছে, সেদিকে এগুতেই আমার মাথায় এল এই আবহাওয়ায় কয়েকটা শিশু কোনভাবেই ঘরের বাইরে আসার কথা নয়।
শব্দ এখন আরও চড়েছে। তবে কেমন বিকৃত শোনাচ্ছে। হাসির শব্দটা একটা অশুভ আওয়াজে পরিণত হয়েছে। পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে নিচের দিকের সিঁড়ি থেকে। আমার খোঁজে আসছে ওরা!
প্রথমবারের মত ভয় পেলাম। ওটা চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেল কয়েক সেকেণ্ডে। দৌড়লাম। বেড়ার তারে লেগে জামা ছিঁড়ল, একটা হিলের জুতোও হারালাম। তবে কেয়ার করলাম না। বৃষ্টির মধ্যে ছিন্ন কাপড় এবং এক পায়ে জুতো পায়ে ছুটতে লাগলাম।
সৌভাগ্যক্রমে টহল পুলিসের একটা গাড়ি আমাকে দেখতে পেয়ে তুলে নিল। শুরুতে ওরা ভাবল, কেউ আমাকে তাড়া করেছে। তবে যখন কী ঘটেছে খুলে বললাম, দয়ালু মালয়ী পুলিস কর্পোরালটি সমঝদারের মত মাথা নাড়লেন। অবাক হননি, জানালেন। প্রাচীন এই স্কুলটা যে ভুতুড়ে এটা নাকি এখানকার অনেকেরই জানা। এ কারণে আশপাশের লোকেরা এই জায়গাটি এড়িয়ে চলে। দালানটা এত বছর ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে কেন, বুঝতে পারলাম এবার।
শেষ বাস
এবারের অভিজ্ঞতাটি শেইলা কো নামের এক স্কুল ছাত্রীর।
এক ছুটির দিনে মেরিন প্যারেডের আয়োজিত এক বারবিকিউ পার্টিতে গিয়েছিলাম স্কুলের বান্ধবীদের সঙ্গে। আমি ছাড়া সবাই রাতে সেখানেই থেকে গেল। আমার বাবা- মা খুব কড়া ধাঁচের। যেখানে ছেলেরাও আছে সেখানে কোনভাবেই রাত কাটাতে দেবেন না আমাকে।
রাত মোটামুটি পৌনে বারোটার দিকে মন খারাপ করে বাস ডিপোতে দাঁড়িয়ে শেষ বাসের অপেক্ষা করতে লাগলাম। অন্ধকার, জনহীন ডিপোতে একাকী দাঁড়িয়ে আছি। তারপর ঠিক মধ্যরাতে শেষ বাসটি এল। তবে এটাকে ঠিক স্বাভাবিক মনে হলো না আমার কাছে।
পুরানো একটা এসবিএস বাস। এত পুরানো এসবিএস বাস আগে দেখেছি বলে মনে পড়ল না। শুধু পুরানো যে তা নয়, ময়লাও। দাঁড়িয়ে পড়ল ওটা। আমাকে ভেতরে ঢুকতে বলল গাড়ির চালক। গাড়ির ধোঁয়াটে জানালা দিয়ে দেখলাম ড্রাইভার প্রায় কঙ্কালের মতই শীর্ণকায়। চোখদুটো কোটরে ঢুকে আছে। ভেতরে কোন বাতি নেই গাড়িটার, তাই ঢোকার সাহস পেলাম না।
তখনই কণ্ডাক্টর হাজির হলো। বলল, ‘বোন, তাড়াতাড়ি ওঠো, সময় নেই আর।’
চালকের চেয়ে তার অবস্থা আরও খারাপ। কেবল যে শরীরে রক্ত-মাংসের বালাই নেই তা নয়, চামড়াটাও কেমন ফ্যাকাসে। মাথার জায়গায় জায়গায় চুল নেই। যখন আমার দিকে তাকিয়ে হাসল আঁতকে উঠলাম। দাঁতগুলো ক্ষয়ে যাওয়া, কালো। বিহ্বলের মত মাথা নাড়লাম। চালককে গাড়ি ছাড়ার ইশারা করল সে। গাড়িটা চলে গেল।
তখনই আমার মনে পড়ল, এসবিএস বাসে কোন কণ্ডাক্টর থাকে না এখন আর। বড় ধরনের কোন ঝামেলা আছে ওই বাসটায়।
তারপরই নতুন, চকচকে একটা বাস এসে দাঁড়াল। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই ট্রান্স আইল্যাণ্ড বাস আমি ঠিক যে স্টেশনে যেতে চাই সেখানেই যাবে। স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললাম। বাসে উঠে কণ্ডাক্টরের কাছে জানতে চাইলাম আগের বাসটার বিষয়ে।
‘কোন্ শেষ বাস? এটাই তো শেষ বাস।’ অবাক হয়ে বলল সে।
ওই অশুভ বাসটায় সে রাতে উঠলে কী হত ভেবে আজও কেঁপে ওঠে আমার শরীর।
গায়ে কীসের দাগ?
ভিনসেন্ট ননিস নামের এক বুড়োর কাহিনী এটা। এ ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তাও বছর বিশেক হয়ে গেল।
গত শতকের পঞ্চাশের দশকে সিঙ্গাপুর টার্ফ ক্লাবে কাজ করতাম। সিঙ্গাপুরের তখন একটা সময়ই গিয়েছে। যুদ্ধের পর পর। যুদ্ধের ফলাফল হিসাবে অনেক সিঙ্গাপুরী আঙুল ফুলে কলা গাছ হয়ে উঠেছে। আমি প্রায়ই ভাবতাম যুদ্ধের কারণে কীভাবে কিছু লোক বড়লোক হয়ে যায়! আমার কাছে একেবারে অসম্ভব মনে হত। তবে ওই লোকদের ধারণা অবশ্যই ভিন্ন ছিল।
যারা লাভবান হয় তাদের মধ্যে আমার পরিচিতদের একজন ছিল ওয়ং কিম সেং। সে পরিণত হয় সিঙ্গাপুর এবং মালয়েশিয়ার ধনী লোকদের একজনে।
টার্ফ ক্লাবে বিশাল এক আস্তাবল ছিল কিমের। সেখানে দামি সব রেসের ঘোড়া থাকত। খুব নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিল সে। বিন্দুমাত্র মায়া-দয়ার বালাই ছিল না মনে। কোন ঘোড়ার রেসে দৌড়নোর মেয়াদ ফুরিয়ে এলে কুকুরের খাবার বানানোর জন্য বেচে দিত, অন্য মালিকেরা যেখানে এমন পরিত্যক্ত ঘোড়াগুলোকে চারণভূমিতে ছেড়ে দিত। তাই তাকে ঘৃণা করতাম রীতিমত। যে কারণে তার এত ধন- সম্পত্তি সেই ঘোড়াগুলোর সঙ্গে কীভাবে এটা করে!
যা হোক, ওয়ং কিম সেং তখন রীতিমত উড়ছে। রুপোলী একটা রোলস রয়েসে চেপে প্রতি সপ্তাহে ছুটির দিনে ক্লাবে আসতে দেখি তাকে। এক কথায় রাজার মতই তার চালচলন।
তবে পঞ্চাশের দশকের শেষ এবং ষাটের দশকের গোড়ার দিকে ভাগ্যদেবী মুখ ফিরিয়ে নিতে লাগল তার দিক থেকে। একের পর এক ব্যবসায় মার খেতে লাগল।
ওই সময়ই তার চেহারায় হতাশ, হতবিহ্বল একটা ভাব লক্ষ করি প্রথমবারের মত। তাকে ঘিরে থাকা বিশাল চাটুকারের দল কমতে কমতে এসে ঠেকেছে কয়েকজনে। এরা তার পোষা দুর্বৃত্ত।
এদিকে আরেকটা গুজব ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। দ্রুতই দেনা পরিশোধ করতে না পারলে তার বেশিরভাগ সহায়- সম্পত্তি নিলামে তুলে দেবে ব্যাঙ্ক। বলা চলে পতনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে সে।
তারপরই আমার চোখের সামনে ঘটল ভয়াবহ সেই ঘটনাটি। সারাদিনের প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর সেদিন রাতে বেরিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম ক্লাব থেকে। এসময়ই দেখলাম কিমের রোলস রয়েস ঢুকছে ভেতরে। এত রাতে গাড়িটাকে দেখে আশঙ্কায় কেঁপে উঠল আমার শরীর। কিম দু’জন সঙ্গীসহ নামল গাড়ি থেকে। চুপিসারে এগিয়ে গেল তারা আস্তাবলের দিকে। পরমুহূর্তেই ঘোড়াগুলোর আতঙ্কিত চিৎকার শুনতে পেলাম। কী হয়েছে দেখতে ঘুরলাম। হায়, খোদা! আগুন লেগেছে আস্তাবলে। দৌড়ে একটা অগ্নি-নির্বাপক তুলে নিলাম। কিন্তু ওটাসহ আস্তাবলের দিকে দৌড়াতেই কিমের লোকেরা পথ আটকে দাঁড়াল।
‘ওখান থেকে দূরে থাকো, বুদ্ধ!’ সতর্ক করে দিল কিম সেং। তাকে পাত্তা না দিয়ে দশাসই গুণ্ডাদুটোকে পাশ কাটিয়ে আগুনের শিখা লক্ষ্য করে অগ্নিনির্বাপকের মুখ তাক করলাম। এসময়ই ঘাড়ে প্রচণ্ড একটা রদ্দা অনুভব করলাম। মাটিতে আছড়ে পড়লাম। কিমের পোষা গুণ্ডাদের একজন পা তুলে দিল আমার ওপর।
‘তোমাকে আমি এসব থেকে দূরে থাকতে বলেছি।’ গর্জে উঠল কিম।
জ্বলতে থাকা আস্তাবলের ধোঁয়ায় নাকি ঘোড়াগুলোর জন্য আমার চোখে পানি চলে এসেছিল, বলতে পারব না। হতভাগা ঘোড়াগুলোর চিৎকার শুনতে পেলাম, আগুনের লেলিহান শিখা ঘিরে ফেলেছে তাদের। তার আস্তাবলটা জ্বলে-পুড়ে একেবারে ছারখার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল বদমাশ লোকটা। তারপর উচ্চস্বরে হাসতে শুরু করল, এখন জানে বীমার টাকায় অনেকটাই আর্থিক সমস্যা সামলে উঠতে পারবে।
ওই সময়ের সিঙ্গাপুরে আইনের তেমন একটা বালাই ছিল না। প্রতিটি জায়গা ছিল দুর্নীতির আখড়া। তাই ঘটনাটা সামাল দিতে খুব একটা বেগ পেতে হলো না কিমকে।
তারপরই অদ্ভুতভাবে যবনিকাপাত হলো কিম অধ্যায়ের। কেউ বলতে পারে না ঠিক কেমন করে ঘটনাটা ঘটল। তবে লোকের মুখে মুখে গল্পটা ছড়িয়ে পড়ল। ওয়ং কিম সেংকে তার বিশাল ভিলার মাঠে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে কোন একটা জন্তুর পাল তার ওপর দিয়ে চলে গিয়েছে। সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার, তার শরীর বা পোশাকের যে টুকরোগুলো উদ্ধার করা সম্ভব হয় তাতে পাওয়া যায় আগুনে পোড়া খুরের ছাপ।
রেলস্টেশনের মেয়েটি
এবারের অভিজ্ঞতাটি জেনিসি লিম নামের এক তরুণীর।
নভেনা মেট্রো রেলস্টেশনে আসা-যাওয়া করা ট্রেনগুলোতে চড়ে সন্ন্যাসিনীর পোশাক গায়ে চাপানো রহস্যময় এক নারীকে চলাফেরা করতে দেখেছেন কেউ কেউ। তবে মেট্রোরেলে দিনে-রাতে নিয়মিত চলাফেরা করলেও তাকে কখনও দেখিনি। হয়তো একদিন ওই অশরীরীর দেখা পেয়েও যেতে পারি।
তবে রহস্যময় একটা স্কুল পড়ুয়া মেয়েকে এক সকালে তোয়া পেয়োহ স্টেশনে এক ট্রেনে দেখেছি। সে কাহিনীটাই বলব।
সিটি হলে যাচ্ছিলাম। আমার সামনে বসেছিল মেয়েটা। তার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েনি আমার। আর পাঁচ-দশটা স্কুল ছাত্রীর মতই মনে হচ্ছিল। তবে চুল অনেক লম্বা, কোমর পর্যন্ত। সাদা একটা ইউনিফর্ম পরনে ছিল তার। তবে খুব ভালভাবে লক্ষ্য করতে পারিনি, কারণ মাথা নিচু করে একটা বই পড়ছিল। লম্বা চুলগুলো মুখের বেশিরভাগটাই ঢেকে রেখেছে।
যখন সিটি হলে পৌঁছল ট্রেন, আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। মেয়েটাকেও উঠতে দেখলাম। তখনই চেহারাটা দেখলাম। মুখের চামড়া তামাটে। তবে অবাক হলাম চোখজোড়া দেখে। ওগুলো প্রায় বর্ণহীন।
তারপরই বিস্ময়কর কাণ্ডটা হলো। এস্কিলেটরে যখন উঠলাম তখন সে ছিল আমার সামনে। কিন্তু যখন ওপরে উঠলাম মেয়েটা সেখানে নেই। চারপাশে তাকালাম তার খোঁজে। কাঁধের পাশ দিয়ে তাকাতেই শিউরে উঠলাম, আমার ঠিক পেছনে মেয়েটা। হাসছে। এটা অসম্ভব। পুরোপুরি ঘুরে আমার পাশ কাটিয়ে যাওয়া ছাড়া কীভাবে এটা করল সে?
যখন টিকেট চেকারের সামনে পৌছলাম ততক্ষণে সে হাওয়া। একটু পরে আবার দেখলাম তাকে, আরও কয়েকজন যাত্রীর সঙ্গে নর্থ ব্রিজ রোডের দিকে যাচ্ছে। অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। তার ওপর চোখ রেখে দ্রুত হাঁটতে লাগলাম। কেবল মেয়েটার থেকে দুই মিটার দূরে, এসময় বাতাসে মিলিয়ে গেল। কীভাবে সে এটা পারল?
এক হপ্তা পরের ঘটনা। আমার মা আর খালার সঙ্গে তোয়া পেয়োহ মেট্রো রেলস্টেশনে এসেছি। তখনই আবার মেয়েটাকে দেখলাম। আরও কিছু যাত্রীর সঙ্গে একটা ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছে। কী ঘটেছে আগেই মাকে বলেছিলাম। এবার ইশারায় দেখালাম। মা ও খালা বিষয়টি তদন্ত করে দেখবে ঠিক করল। মেয়েটার দিকে আস্তে-ধীরে হাঁটতে লাগল তারা।
কিন্তু যখনই মেয়েটার কাছাকাছি হলো, তাদের দিকে রংহীন চোখে কতক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর আগের মতই বাতাসে উবে গেল।
সু নামের ছেলেটি
লি থাই হোং নামের এক যুবকের গল্প।
একসময় আর্মিতে চাকরি করতাম। এক শনিবার বিকালে আমার পুরানো অফিসার লেফটেনেন্ট লও কুইয়ি ইয়ং, আমি এখন যে অ্যামিউজমেন্ট পার্কে কাজ করি সেখানে এলেন। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী এবং ছেলে। আমরা গল্প করছিলাম, এদিকে তাঁর স্ত্রী আর ছেলে বিভিন্ন রাইডে চড়ছিল। স্ত্রী আর ছেলেটার সঙ্গে তখন আমার পরিচয় করিয়ে দেন। ভদ্রমহিলার নামটা ভুলে গেছি। তবে ছেলেটার নাম মনে আছে স্পষ্ট। সু নামের একটা ছেলের নাম কী করে ভুলি?
‘কী অদ্ভুত!’ বলে ফেললাম, ‘এটা তো মেয়ের নাম!’ বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুইয়ি ইয়ং ব্যাখ্যা করলেন। অন্য এক নারীর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছিল তাঁর। কিন্তু ভয়াবহ এক দুর্ঘটনায় সে মারা যায়। শুরুতে খুব ভেঙে পড়লেও বর্তমান স্ত্রীর সঙ্গে ঘটনাচক্রে দেখা হয়ে যাওয়ার পর ধীরে ধীরে আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন। সাবেক প্রেমিকার কথাও ভুলে যান। বিয়ের কথাও পাকা হয়।
ঠিক ওই সময় হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েন কুইয়ি ইয়ং। বেশ কয়েকজন চিকিৎসক দেখিয়েও লাভ হলো না। একপর্যায়ে এক ওঝার শরণাপন্ন হলো পরিবারটি।
তিনিই জানালেন পুরানো প্রেমিকার প্রেতাত্মা সওয়ার . হয়েছে তাঁর ওপর। অন্য একজনকে বিয়ে করতে যাচ্ছে তার প্রেমিক এটাই তাকে অশান্ত করে তুলেছে। এর একমাত্র সমাধান ভূত বিয়ে।
অসুস্থ কুইয়ি খুব একটা বাধা দিতে পারেননি। তাঁর কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবারের সদস্যরা পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করে। একটা প্রথাগত ছোটখাট চীনা বিয়ের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যেখানে মেয়েটার প্রতিনিধিত্ব করে তার পরিবারের কালপঞ্জি লেখা একটা ফলক।
আশ্চর্য ব্যাপার! বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষের অল্প সময়ের মধ্যে কুইয়ি ইয়ং সুস্থ হয়ে ওঠেন।
পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারলাম না এই বর্ণনায়। জিজ্ঞেস করলাম, ‘এই সামান্য ব্যাপারটা কি ওই প্রতিহিংসাপরায়ণ আত্মাটাকে ঠাণ্ডা করে দিল, যেখানে পরে তোমার পছন্দের পাত্রীকে ঠিকই বিয়ে করে সংসার করতে লাগলে?’
আবারও দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইয়ং বললেন, ‘ঠিকই বলেছ। ব্যাপারটা এতটা সহজ নয়। আমাকে ওঝার কথামত প্রতিজ্ঞা করতে হয় প্রথম বাচ্চাটার নাম আমার প্রাক্তন প্রেমিকার নামে রাখব। তাই ওর নাম সু।’
ওই সময়ই সু নামের ছেলেটা আমার কাছে এসে বলল, ‘হ্যালো, আঙ্কেল!’
যেভাবে সে কথা বলল, হাঁটল, চোখের পলক ফেলল, বুক কেঁপে উঠল আমার। সব কিছু অবিকল একটা মেয়ের মত। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম, আমার আশঙ্কা যেন সত্যি না হয়।
শিস বাজায় কে?
স্টিভেন গোহ নামের এক তরুণের কাছ থেকে এবারের কাহিনীটি সংগ্রহ করা।
আমাকে গুরুজনরা বলেছিল, অন্ধকারে গোরস্থানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শিস বাজানো উচিত নয়। কারণ এটা মৃতদের আকর্ষণ করে। তবে এসব গালগপ্পে মোটেই বিশ্বাস নেই আমার। উল্টো ঠিক করলাম মওকা বুঝে একদিন এটা পরীক্ষা করে দেখব।
জালান বাহার গোরস্থানের কাছেই আমার বাসা। এক নিরানন্দ শনিবার। হাতে কোন কাজ নেই। হঠাৎ দুষ্টবুদ্ধিটা মাথায় চাপল। মধ্যরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। তারপর বাইসাইকেল চালিয়ে রওয়ানা হলাম গোরস্থানের দিকে। কাছাকাছি এসে সাইকেল থেকে নেমে পড়লাম। এবার সারি সারি সমাধির মাঝখান দিয়ে সাইকেলটা ঠেলতে ঠেলতে এগুলাম। রাস্তাটা প্রচণ্ড অন্ধকার। তবে একটুও ভয় করছে না আমার।
একসময় শিস বাজাতে শুরু করলাম।
চারপাশ একেবারে সুনসান। আমার পায়ের আওয়াজ ছাড়া আর কোন শব্দ কানে আসছিল না। এখন যোগ হয়েছে আমার শিসের আওয়াজ। তারপরই ওটা শুনলাম। আমার পেছন থেকে চাপা একটা শ্বাস নেয়ার শব্দ। ওটা কিছু না ধরে নিয়ে, শিস দিতে শুরু করলাম আবারও।
তারপরই গা-টা শিরশির করে উঠল, আমার পেছনে মৃদু একটা শিসের শব্দ। বেশ অদ্ভুত, তবে সুখ ছড়ানো একটা সুর। কেমন ভেজা ভেজা। এবার ভয় পেলাম। শিস বাজানো বন্ধ করে দিলাম। তবে এখন আরও কাছাকাছি চলে এসেছে শিসের শব্দ। আর একজন-দু’জন নয় গোটা একটা দল যেন যোগ দিয়েছে এতে। চারপাশের সমাধিগুলো থেকেও আসছে একই সুরে শিসের আওয়াজ। তখনই সাইকেলে চেপে এক টানে বেরিয়ে এলাম গোরস্থান থেকে। ভূতবিষয়ক প্রাচীন লোককিচ্ছাগুলো এরপর থেকে বিশ্বাস করতে শুরু করি।
জ্যান্ত কবর
হ্যাম্পস্টিডের ওয়াল ওয়াক-এর বেশ কাছেই তিনতলা একটা বাড়ি। চারপাশে বেশ কতকটা জায়গায় আর কোন অট্টালিকা নেই। এটি, ‘দ্য ডিকনস’ নামেও পরিচিত। ভুতুড়ে বলে বাড়িটির বদনাম আছে বহু আগে থেকে। অনেক লোকই এর শিকার হয়েছেন। তবে এদের মধ্যে এক অধ্যাপক এবং এক লেখকের অভিজ্ঞতাটাই সবচেয়ে রোমাঞ্চকর ও লোমহর্ষক। একটা গবেষণার প্রয়োজনে একরাত একসঙ্গে এখানে কাটান দু’জনে। লেখকের বর্ণনাতেই তাঁদের সে রাতের অভিজ্ঞতা তুলে ধরছি।
আমাদের অভিযান শুরু করি একতলার পেছনের এক কামরা থেকে, রাত দশটার দিকে। তবে এখানে অনুসন্ধান চালানোর জন্য বাড়ির মালিকের অনুমতি জোগাড়ে যথেষ্ট কাঠ-খড় পোড়াতে হয় আমাদের। আমার স্ত্রী যদি তাঁর পুরানো বন্ধু না হত তাহলে হয়তোবা এটা সম্ভবই হত না। বাড়িটাকে বাছাই করার একটা কারণ এর পরিবেশটাই অন্য রকম, ভৌতিক ঘটনার জন্য অধিকতর মানানসই। দ্বিতীয়ত এর ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোগুলোর একটা বারান্দামুখী। বেশি বিপদ হলে ওই পথে নিচের নরম মাটিতে লাফিয়ে পড়তে পারব আমরা। এখানে একটা বিষয় স্বীকার করে নেয়া উচিত, মানুষ হিসাবে আমি অসম্ভব ভীতু প্রকৃতির। তবে অধ্যাপকের প্রতি আমার অগাধ আস্থা। আমার মনে তাঁর সাহস নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই। ভয়ানক পরিস্থিতিতেও তিনি ঘাবড়ে যাবেন বলে মনে হয় না। যদ্দূর জানি ভূত বা প্রেতাত্মা নিয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতাও আছে তাঁর। তিনি নাকি এদের গতিবিধি টের পেয়ে যান আগেই।
মূল কাহিনীতে ফিরে আসা যাক। পেছনের ওই কামরাটায় মোটামুটি আধ ঘণ্টা হলো বসে আছি এমন সময় সিঁড়ির বাইরে একটা পদশব্দ শুনলাম বলে মনে হলো। প্রফেসর বললেন, এটা কেবল কাঠের ক্যাচক্যাচ আওয়াজ। তারপর কাঠ ও ধাতব পদার্থের সম্প্রসারণ বিষয়ে নাতিদীর্ঘ এক বর্ণনা দেয়া শুরু করলেন। একপর্যায়ে তাঁকে বললাম বহু বছর আগে স্কুলরুমেও এ ধরনের আওয়াজ শুনেছি। তারপর চুপচাপ বসে, আইভি লতার ছায়াগুলো চাঁদের আলোয় মেঝেতে খেলা করছে তা দেখতে লাগলাম। একই সঙ্গে যে কোন ধরনের শব্দ আমার দৃষ্টি ওদিকে নিয়ে যাচ্ছে।
তারপরই হঠাৎ পথ ধরে প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে আসা ঘোড়ার খুরের এবং গাড়ির চাকার আওয়াজ পেলাম। একপর্যায়ে আশ্চর্য হয়ে আবিষ্কার করলাম ঘোড়ার গাড়ি বা যেটাই হোক সেটা ‘দ্য ডিকনস’-এর দিকেই ঘুরে গিয়েছে। এরপরই বাড়ির সামনের পথের পাথরে শব্দ হলো এবং পরক্ষণেই সদর দরজায় জোরে কড়া নাড়ার আওয়াজ। কিন্তু বাড়িতে যখন ঢুকি তখন দেখেছিলাম সদর দরজায় কোন কড়া নেই। একটু ভয় পেয়ে গেলাম। তবে প্রফেসরের দিকে যখন তাকালাম ওই রাতে সত্যিকার অর্থে প্রথম ধাক্কাটা খেলাম। দরজায় নক করার আগে নিজের চেয়ারে গা এলিয়ে শুয়ে ছিলেন। চেহারায় ছিল প্রশান্তির একটা ছাপ। এ সব কিছুই এখন বিদায় নিয়েছে। আমূল একটা পরিবর্তন এসেছে। একেবারে সোজা হয়ে বসে আছেন এখন, সাধারণ আকারের দ্বিগুণ হয়ে গেছে চোখজোড়া, খোলা দরজার দিকে তাকিয়ে আছেন ড্যাব ড্যাব করে। হাতজোড়া চেয়ারের হাতল আঁকড়ে ধরে আছে।
তাঁর চেহারার এমন পরিবর্তন দেখে আমার রক্ত হিম হয়ে গেল। এদিকে বেশ কিছুটা সময় চলার পর দরজার শব্দটা এখন থেমে গিয়েছে। সদর দরজা খুলে কিছু একটা এগিয়ে আসার মৃদু শব্দ পেলাম।
এই চালমাত অবস্থায় প্রফেসর আবারও আমাকে চমকে দিলেন। চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে জানালার দিকে দৌড়লেন, সেখান থেকে বারান্দায়, ওই শেষবারের মত দেখলাম তাঁকে আমি।
স্বীকার করতে দোষ নেই ক্ষমতা থাকলে তাঁকে অনুসরণ করতাম। কিন্তু ভয়ে এতটাই অবশ হয়ে গিয়েছে হাত-পা এমনকী গোটা শরীর, নড়তে পারছি না। কেবল আতঙ্ক নিয়ে অতিপ্রাকৃত একটা কিছুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। ওটা কী? কী দেখব আমি? জিনিসটা কীভাবে ভেতরে ঢুকল?
ঈশ্বর! যাঁরা এই পরিস্থিতিতে পড়েছেন তাঁরাই কেবল ওই সময়ে একজন মানুষের মনের অবস্থা কী হয় তা বুঝবেন। একটার পর একটা সেকেণ্ড পেরোতে লাগল। কিছুটা সময় তেমন কিছুই ঘটল না। তারপরই ধীরে ধীরে কুয়াশার একটা ঘেরাটোপ গোটা কামরাটাকে ঢেকে দিতে লাগল। মেঝের ছায়াগুলো অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল। সিঁড়িতে খুব মৃদু একটা পদশব্দ শুনলাম। আসছে ওটা। নড়ার চেষ্টা করলাম, দৌড়নোর চেষ্টা করলাম, দৃষ্টিটা দরজা ও ল্যাণ্ডিঙের দিক থেকে সরিয়ে নিতে চাইলাম। কিন্তু পারলাম না।
পদশব্দ ধীরে ধীরে আমার আরও কাছে আসতে লাগল। একপর্যায়ে সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে গেল। আমার বরাবর ল্যাণ্ডিঙে দাঁড়িয়ে আছে এখন, স্পষ্ট বুঝতে পারছি। একসময় কামরাটায় প্রবেশ করল। তবে এখনও কিছু দেখতে পাচ্ছি না। যখন এগিয়ে এল, দুটো আলাদা গোলাকার আলো দেখতে পেলাম। ধীরে ধীরে দুটো অনিন্দ্যসুন্দর হাতে রূপ নিল। সরু, লম্বা, সাদা আঙুল, গোলাপী নখগুলো পালিশ করা। অনেকগুলো আংটি আঙুলে। হীরা, রুবি, পান্নার মত দামি রত্নপাথর ঝকঝক করছে তাতে। যখন হাতজোড়া আমার কাছাকাছি হতে লাগল, মিষ্টি, মাতাল করা একটা গন্ধ চাবুকের মত আছড়ে পড়ল আমার নাকে। কেউ একজন আমার ওপর ঝুঁকে পড়েছে। দামি পশমী গাউনের ছোঁয়া অনুভব করছি। নরম একটা হাত আমার গলা জড়িয়ে ধরল। উষ্ণ, সুগন্ধি একটা ঠোঁটের স্পর্শ পেলাম ঠোঁটে। ওই নরম আঙুলগুলো আমার গাল, কপাল, চোখে আদরের স্পর্শ বুলিয়ে দিতে লাগল। সব ভয় দূর হয়ে গেল মন থেকে।
‘হায়, ঈশ্বর!’ উল্লাসে মনে মনে চেঁচিয়ে উঠলাম, ‘এটা যদি চলতেই থাকত আজীবন, তবে কী ভালই না হত!’
নরম আঙুলগুলো এবার মুখ হাঁ করাল আমার। নরম, শীতল একটা তরল নেমে গেল আমার গলা দিয়ে। চেয়ারে মাথাটা ঠেস দিয়ে রাখলাম। কপালে নরম, আদুরে একটা হাতের স্পর্শ। এই স্পর্শে ধীরে ধীরে ঘুমের অতল রাজ্যে তলিয়ে গেলাম। যখন জাগলাম, আবারও ওই স্পর্শ, মাতাল করা গন্ধের জন্য পাগল হয়ে গেলাম।
‘ফিরে এসো!’ করুণ কণ্ঠে মিনতি করলাম, ‘এক মুহূর্তের জন্য হলেও তোমার সেই স্বর্গীয় স্পর্শ চাই।’ কিন্তু কোন উত্তর পেলাম না। তারপরই আবিষ্কার করলাম কথা বলতে পারছি না। যেমন নড়াতে পারছি না শরীরটা। একটা বিছানায় শুয়ে আছি। কামরায়ও একা নই আর।
আমি দেখতে না পেলেও একাধিক মানুষ বা প্রেতাত্মা আমার কাছেই দাঁড়িয়ে আছে।
দাঁড়িয়ে আছে। আমার মৃত্যু এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়েই আলোচনা করছে তারা। কর্কশ এক জোড়া হাত নির্মমভাবে আমার শরীর মাপছে কফিনে ঢোকানোর জন্য। একপর্যায়ে সেটায় ঢোকানো হলো। পেরেক ঠুকে কফিনের ডালা আটকানো হচ্ছে এখন। নড়ার এবং চিৎকার করার প্রাণান্তকর চেষ্টা করছি। কিন্তু যেখানে শুইয়ে রাখা হয়েছে সেখানেই পড়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করা সম্ভব হলো না। কফিনের কাঠের কেমন গা গুলানো মিষ্টি একটা গন্ধে রীতিমত বমি পাচ্ছে।
তারপর দুই জোড়া হাত কফিনটা তুলে নিল। সিঁড়ি বেয়ে আমাকেসহ নামতে লাগল তারা। ঘোড়ার গাড়িতে তোলা হলো আমার দেহসহ কফিনটা। বুঝতে পারলাম গাড়ির নড়াচড়া এবং ঘোড়াগুলোর হেষা শুনে। তারপর দুলে উঠল আমার শরীরটা। পাথুরে রাস্তায় চলতে শুরু করেছে গাড়ি। কিছুক্ষণ হুঁশ ছিল না। একপর্যায়ে যখন জ্ঞান ফিরল, ভয়াবহ একটা বাস্তবতার সামনে হাজির হলাম। জীবন্ত কবর দেয়া হয়েছে আমাকে।
আবিষ্কারটা এতটাই ভয়াবহ যে জ্ঞান হারালাম। তবে মাটির শীতল, দম বন্ধ করা পরিবেশের কারণে জ্ঞান ফিরে পেলাম আবার। সব ঘটনা একের পর এক মনে পড়তে লাগল।
প্রচণ্ড একটা হতাশা প্রভাব বিস্তার করল আমার ওপর। যে কোন শব্দ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠলাম। কিন্তু চোয়াল নাড়াতে পারলাম না। হাতদুটো ছুঁড়লাম। ওগুলো নাড়াতে পারছি এখন। তবে মুখের একটু ওপরে, আমার কাঠের কারাগারের ছাদে বাড়ি খেল ও-দুটো। মাথা ঝাঁকালাম। পা ছুঁড়তে লাগলাম। একপর্যায়ে পায়ের আঙুল ভাঙল। ফেনা, রক্ত মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। হতাশ, পর্যুদস্ত আমি হাল ছেড়ে দিলাম।
তারপর অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো। ওপরের অন্ধকারের সমুদ্রটা যেন বুকে ইটের বোঝার মত চেপে আছে। হাঁসফাঁস করতে করতে হাত দিয়ে ওটা সরাবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলাম।
আরও একবার স্থির হয়ে গেলাম। মৃত্যুর পর কি এভাবেই অন্ধকার ঘিরে ধরে চারপাশ থেকে? তারপরই আগের জীবনের কথা, সেখানে একের পর এক ভুলের কথা স্মরণ করলাম। পাপের কথা ভাবলাম। আহ্! একবার যদি মুক্তি পেতাম জীবনটাকে আবার নতুন করে সাজাতাম। গোরস্থানের ওপরের বাতাসটাকে অনেক মিষ্টি, তাজা, আর ঘাসগুলোকে সবুজ মনে হচ্ছে। একবার যদি সেখানে, পৌঁছতে পারতাম!
নিজের বন্ধুদের কথা ভাবলাম। আমি যে বেঁচে আছি তা যদি জানাতে পারতাম তাদের। কী খুশি হত তারা! ভাবত চিকিৎসক ভুল করেছেন। তাদের বন্ধু শ্বাস নিতে পারছে। দ্রুত তারা দৌড়ে আসত আমাকে বাঁচাতে। তারপরই নির্মম সত্যটা উপলব্ধি করতে পারলাম। আমার অবস্থা তাদের জানানোর কোন সুযোগই নেই। এখানেই একাকী মরতে হবে আমাকে। চোখ বন্ধ করেই যেন গোরস্থানের চারপাশের কাদাটে মাটির স্তূপ, দু’পাশের সমাধিগুলো দেখতে পাচ্ছি। আশ্চর্য ব্যাপার ওগুলোর ভিতরটাও দেখতে পাচ্ছি। দাঁতহীন, ধূসর চুলের ওই মহিলা, ওই বাচ্চাটার খুদে আধো বিকশিত কঙ্কাল। একটার পর একটা সারি ধরে প্রত্যেককেই দেখতে পাচ্ছি। তাদের দিকে তাকাতেই দেঁতো হাসি দিচ্ছে। কেঁপে উঠছি। আবার তাকাতেই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তারপরই দেখলাম বীভৎস চেহারার একটি অদ্ভুত ধরনের প্রাণী গড়িয়ে গড়িয়ে শরীর মুচড়ে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে। শরীরটা হলুদ। একসময় পৈশাচিক জিনিসটা আমার পা স্পর্শ করল। ওই পর্যায়ে জ্ঞান হারালাম। মনে হলো যেন বহু সময় পর জ্ঞান ফিরে এল আবার। চোখ খুলতেই নিজেকে আবিষ্কার করলাম ‘দ্য ডিকনস’-এর খোলা জানালাগুলোর পাশে বসা অবস্থায়।
ওখানে বসার চেষ্টা করিনি আর কখনও, এক রাতের অভিজ্ঞতাই আমার জন্য যথেষ্ট। এই বাড়ির পুরানো বাসিন্দাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হলো আমাকে। শেষ পর্যন্ত সফল হলাম। এদের দু’জন মি. ডি কোসার্ট এবং মিসেস স্মিথ আমাকে দেখতে এলেন একই সকালে।
প্রথমে এলেন ডি কোসার্ট। লম্বা, হালকা-পাতলা গড়নের এক মানুষ। মাঝবয়সের ভদ্রলোকটি মরিচা-কালো রঙের একটা স্যুট পরে আছেন।
‘আপনার কাছ থেকে কিছু জানার আছে আমার, ডিকনস সম্পর্কে।’ কথাটা বলে একটা চেয়ারে বসার ইশারা করে দরজাটা সাবধানে আটকে দিলাম। পাছে আবার আমার বাক্যবাগীশ ল্যাণ্ডলেডি কিছু শুনে ফেলে।
‘ঠিক বলেছেন। বছর তিনেক আগে দু’বছরের চুক্তিতে ‘দ্য ডিকনস’ লিজ নিই। মাত্র এক রাতই সেখানে কাটাতে পারি। আর কাছেধারেও যেতে চাই না জায়গাটির। কয়েক বছর আগে স্ত্রী গত হয়েছে আমার। বাড়িতে আমার সঙ্গে যান রাশভারী বয়স্ক এক হাউসকিপার, একজন রাঁধুনি ও একজন মেইড। দশটার দিকে সবাই যার যার বিছানায় চলে যাই আমরা। তখন মধ্যরাত। অনেক চেষ্টা করেও ঘুমাতে পারছি না। এসময় করিডোরে একটা পায়ের আওয়াজ পাই। ওটা আমার দরজার দিকেই এগিয়ে আসছে। এদিকে ওই সময়ই ওপর থেকে একের পর এক ধুপধাপ শব্দ শুনলাম।
‘ভাবলাম হাউসকিপার ওপরের কোন সমস্যার ব্যাপারে বলতে আসছে। ড্রেসিং গাউনটা গায়ে চাপিয়ে দরজার দিকে দৌড়লাম। ওটা হাউসকিপার নয় মোটেই, কিন্তু,’ এতটুকুন বলে ভয়ার্ত চোখে আমার দিকে তাকালেন একবার, তারপর আবার শুরু করলেন, ‘বিশালদেহী, আলখেল্লা পরিহিত এক লোক। বুনো, জ্বলজ্বলে চোখ, বসা কপাল, রক্তলাল চোখ। আমার দিকে হাত তুলল সে। বাতাসে নড়ছে আঙুলগুলো। লক্ষ্য করলাম ওগুলোর আগা ভাঙা, রক্ত ঝরছে।
‘ওটা যে একটা প্রেতাত্মা বুঝতে অসুবিধা হলো না, তবে আমাকে আঘাত করতে আসেনি, বরং কোন বিষয়ে সতর্ক করে দিতে চাচ্ছে। তারপরই অদৃশ্য হলো কাঠামোটা। পরমুহূর্তেই এক নারীর দুটো বাহু গলা পেঁচিয়ে ধরল আমার। বিছানায় নিয়ে গিয়ে আদর করে ঘুম পাড়িয়ে দিল। তারপর যখন ঘুম ভাঙল, কিংবা ভাবলাম জেগে উঠেছি, আবিষ্কার করলাম জ্যান্ত কবর দেয়া হচ্ছে আমাকে। সত্যি জ্ঞান ফিরে পেলাম সকালে, যখন মেইড আমার জন্য গরম পানি নিয়ে এল।
‘বিষয়টা আমাকে এতটাই নাড়া দিল যে আশপাশের প্রতিবেশীদের কাছে খোঁজ-খবর নিলাম লোকটির চেহারার বর্ণনা দিয়ে। দেখলাম মি. রবার্ট ভ্যালেন্টাইন ফার্নিস নামের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে। এই বাড়িতেই মারা গিয়েছেন আমি বাড়িতে ওঠার কিছুদিন আগে। তাঁর আত্মীয়- স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তাদের সঙ্গে ভদ্রলোকের খুব একটা দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না অনেক দিন ধরেই। তবে আমার দুঃস্বপ্ন তাদের নাড়া দিল ভীষণ। আবার কবর খুঁড়ে বের করা হলো তাঁর মৃতদেহ। তখনই প্রমাণ পাওয়া গেল জীবন্ত কবরের ঘটনার। তাঁর পাকস্থলীর ভেতরের জিনিস পরীক্ষা করতেই প্রমাণ মিলল ঘুম পাড়িয়ে দেয়ার মত খুব শক্তিশালী মাদকের। ওই মাদকের কারণেই কোমায় চলে যান। সবাই ধরে নেন ভদ্রলোক মারা গিয়েছেন। জীবন্ত কবর দেয়া হয় তাঁকে। অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে দেখতে এসেছিলেন যে চিকিৎসক তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়নি। এদিকে তাঁর বিধবা স্ত্রী কোথায় আছে এটাও জানতে পারলাম না।
‘মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে পরে আর দেখা হয়নি। তারপর একসময় ইতালির তুরিনে যাই। সেখানে এক সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে পরিচয় হয়।
‘তার চেহারার, তবে এর চেয়েও বেশি হাতদুটোর প্রেমে পড়ি আমি।’ কেঁপে উঠলেন ডি কোসার্ট। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘দ্য ডিকনস-এ যে হাতদুটো আমায় জড়িয়ে ধরেছিল ঠিক সেগুলোর মতই। কিছুদিনের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল আমাদের। কয়েকদিন যেতে না যেতেই আমার সব সম্পত্তি তার নামে লিখে দেয়ার জন্য চাপ দিতে আরম্ভ করল। এখন আর ওই হাতদুটো সোহাগ করে না আমাকে। রাতে ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠি।’
‘কিন্তু তা কী করে সম্ভব? আচ্ছা, স্যর, আপনার কাছে কি আপনার স্ত্রীর কোন ছবি আছে?’ জানতে চাইলাম।
‘হ্যাঁ, সঙ্গেই আছে। আমার মনে হয়েছিল আপনি দেখতে চাইতে পারেন, লেখকদের কৌতূহল বেশি থাকে জানি আমি,’ এই বলে একটা ছবি এগিয়ে দিলেন।
ওটা পরীক্ষা করতে যাব এমন সময় দরজায় মৃদু একটা টোকার শব্দ। মিসেস স্মিথ নামে এক কৃষ্ণাঙ্গ, হালকা-পাতলা গড়নের মহিলা ভেতরে প্রবেশ করলেন। ডি কোসার্ট যাওয়ার জন্য উঠলেন। এদিকে মহিলাটির ততক্ষণে ছবিটির দিকে চোখ পড়েছে। চেঁচিয়ে উঠলেন উত্তেজনায়, ‘ওহ্, খোদা! এটা কি মিসেস ফার্নিস নয়?’
‘আপনি কি একে চেনেন?’ এই বলে ছবিটা ভদ্রমহিলার সামনে ধরলেন।
‘আপনিই কি সেই লেখক?’ মিসেস স্মিথ হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন।
‘না, আমি এই মহিলার স্বামী।’
‘কিন্তু ইনি তো মিসেস ফার্নিস। তাই নয় কি?’ আমার টেনে দেয়া আসনটায় বসতে বসতে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রমহিলা।
এই মুহূর্তে আমার একটু ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন বলে মনে করলাম। ডি কোসার্টের উদ্দেশে বললাম, ‘মিসেস স্মিথও আপনার মত ‘দ্য ডিকনস’-এর ব্যাপারে আগ্রহী। তাই তিনি আজ সকালে এখানে এসেছেন। তাঁর কী বলার আছে বরং শোনা যাক।’ তারপর মহিলার দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘ম্যাম, আপনি সব কিছু খুলে বলুন। আমার মত এই ভদ্রলোকেরও ওই বাড়ি নিয়ে অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আছে।’
‘তবে,’ বলা শুরু করলেন মিসেস স্মিথ, ‘যা বলব এটা নিয়ে আমাকে কোন ঝামেলায় ফেলবেন না তো আবার! অবশ্য তাতেও খুব একটা কিছু আসে-যায় না। কারণ খুব দ্রুতই এ পৃথিবীর মায়া কাটাতে হবে আমাকে। আমার স্তন, গলা ও একটা ধমনীর ঠিক ওপরে—মোট তিন জায়গায় ক্যান্সার ধরা পড়েছে। চিকিৎসক বলেছেন ভাল হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।’ কথাগুলো বলে একটু সময় চুপ করে থাকলেন ভদ্রমহিলা। হয়তো নিজেকে প্রস্তুত করলেন। তারপর বলতে লাগলেন, ‘আমি বাস করতাম হ্যাম্পস্টিডে। তিন বছর আগে স্বামীকে হারাই। ব্রাইট’স ডিজিজে (কিডনির এক ধরনের রোগ) মারা যান তিনি। এর কিছুদিন আগেই লণ্ডি দিয়েছিলাম একটা। সেই সূত্রে মিসেস ফার্নিসের সঙ্গে যোগাযোগ। ‘দ্য ডিকনস’-এ থাকতেন ভদ্রমহিলা। আমার স্বামীর রোগের ব্যাপারে প্রথম দিন থেকেই তাঁর অদ্ভুত একটা আগ্রহ দেখি। তবে এটায় খুব একটা গুরুত্ব দিইনি প্রথমে। তারপরই একদিন আমার বাসায় হাজির হলেন হঠাৎ। আমার ছোট্ট পার্লারটিতে ডেকে নিয়ে বললেন, ‘আমার মনে হয় স্বামীর অসুস্থতার পেছনে বড় ধরনের খরচ হয় তোমার।’
‘হ্যাঁ, ম্যাম। কুলাতে পারছি না একেবারেই।’ অ্যাপ্রনের কোনা দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললাম।
‘তার কি সুস্থ হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে?’
‘না, ম্যাম। ডাক্তার বলেছেন আর বড়জোর কয়েকটা দিন।’
‘ডাক্তার কয়দিন পর পর আসেন?’
‘আমি ডাকলে তবেই আসেন।’
‘এবার তাঁর পেলব হাতটা দিয়ে আমার কাঁধ স্পর্শ করে গলা নামিয়ে বললেন, ‘তোমার অবস্থাটা আমি বুঝতে পারছি। কিছু টাকা-কড়ি পেলে নিশ্চয়ই ভালই হয়। একশো পাউণ্ড হলে চলবে?’
‘স্বীকার করলাম আমার মত এক দরিদ্র নারীর জন্য একশো পাউণ্ড বিশাল ব্যাপার।
‘খুব ভাল।’ মিষ্টি হেসে বলতে শুরু করলেন, ‘এর বিনিময়ে আমি চাইব তোমার স্বামীকে মৃত্যু পর্যন্ত বাকি কয়েকটা দিন আমার বাড়িতে এনে রাখো। আমি তোমাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি দ্য ডিকনস-এ তার ভালমতই দেখাশোনা হবে। আর তুমি তো বলেছই বড়জোর কয়েকটা দিন বাঁচবে সে। কোথায় মারা গেল এটা নিশ্চয়ই তোমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। মারা যাবার পর তোমার বাড়িতে গোপনে নিয়ে আসা হবে মৃতদেহ। এখান থেকেই গোর দিতে নিয়ে যেতে পারবে। কেউ বিন্দুমাত্র সন্দেহ করবে না।’
‘প্রস্তাবটা এতটাই অস্বাভাবিক যে, কী বলব বুঝে উঠতে পারলাম না।‘
‘কিন্তু, ম্যাম, তুমি কেন এটা করছ?’
ওহ! আমি বললেও বুঝবে না।’ রহস্যময় একটা হাসি দিয়ে বললেন তিনি, ‘এখন একশো পাউণ্ড কামাতে চাইলে রাজি হয়ে যাও।’
‘আমি জানি মিসেস ফার্নিস কথা দিয়ে না রাখার মানুষ নন। কাজেই রাজি হয়ে গেলাম। আমার স্বামীকে সব কিছু বলতে আপত্তি করলেন না। আসলে তাঁর হারানোর কিছু নেই। ভাবলেন এতে যদি আমাদের কিছুটা উপকার হয়! আমি আর আমার ছেলে জিম রাতের আঁধারে স্মিথকে ‘দ্য ডিকনস-এ নিয়ে গেলাম। তিন রাত পর তাঁর মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে এলাম। ডাক্তার জানালেন তাঁকে খবর দিয়েও কোন লাভ হত না। কারণ কোন কিছুই আমার স্বামীকে বাঁচাতে পারত না। একশো পাউণ্ড পেলাম আমরা। মুখ বন্ধ রাখলাম আমি আর আমার ছেলে। তবে একটা বিষয় জেনে আমাদের মনটা বেশ খচখচ করতে লাগল। মি. ফার্নিস নাকি আমার স্বামী যে সময় মারা গিয়েছেন তখনই মারা যান এবং ওই একই রোগে।’
ডি কোসার্টের সঙ্গে চোখাচোখি হলো আমার। ঘৃণায় রি রি করছে আমাদের শরীরটা।
‘আপনি নিশ্চিত মি. ফার্নিস ব্রাইট’স ডিজিজে মারা গিয়েছে?’ জানতে চাইলাম।
‘আমি তাই শুনেছি,’ কাঁধ ঝাঁকিয়ে জবাব দিলেন মহিলা, ‘কয়েকজনই একই কথা বলেছে। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় তেমন কেউ ছিল না। কেবল মিসেস আর ভাড়ায় শোক করা কয়েকজন মানুষ। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে মনে হয় ভদ্রলোকের বনিবনা ছিল না। আমি আর জিম বিষয়টি ভুলতে পারিনি। অনেক সময়ই ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখি। বেশিরভাগ সময় জ্যান্ত গোর হওয়ার দৃশ্য এবং মিসেস ফার্নিসের সাদা, পেলব হাতজোড়া দেখি।’
‘এখন আপনি কী ভাবছেন, মিসেস স্মিথ?’ জানতে চাইলাম আমি, ‘আপনার নিশ্চয়ই একটা অনুমান আছে?’.
‘আমার মনে হয়,’ অনুতপ্ত কণ্ঠে বললেন মিসেস স্মিথ, ‘হতভাগা মি. ফার্নিসের বদলে ডেথ সার্টিফিকেট নিতে ব্যবহার করা হয়েছে আমার স্বামীকে। ডাক্তারকে হঠাৎ ডেকে পাঠিয়েছিলেন মিসেস, আর ভদ্রলোক এখানে যে চাতুরীর আশ্রয় নেয়া হচ্ছে জানতেনও না। ভাবেন সঠিক ডেথ সার্টিফিকেট দিচ্ছেন।
‘তারপর আবার একটা অদল-বদল হয়। আমার স্বামীর মৃতদেহ বাড়িতে আনা হয়। সত্যিকারের মি. ফার্নিসকে দ্য ডিকনস থেকে নিয়ে গিয়ে সমাধিস্থ করা হয়। তবে আমি এখানে বসে আছি এ ব্যাপারটা যেমন নিশ্চিত তেমনি নিশ্চিত তাঁকে জীবন্ত কবর দেয়া হয়েছে। ওই শয়তান মহিলা কোন উদ্দেশ্যে এই চাতুরীর আশ্রয় নেয়। গত তিন বছর ঘটনাটা চেপে রেখেছি বিশাল এক বোঝার মত। এখন বুকটা হালকা লাগছে।’
‘আপনার সন্দেহই সত্যি, মিসেস স্মিথ। তাঁকে জীবন্তই কবর দেয়া হয়েছে। তবে আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এটা গোপনই রাখব। যেমন গোপন থাকবে আমি এক খুনিকে বিয়ে করেছি।’ বললেন ডি কোসার্ট।
ভুতুড়ে বাড়ি মন্টিক্রিস্টো
রায়ানরা বলে অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে ভুতুড়ে বাড়ি হলো মন্টিক্রিস্টো। অলিভ রায়ান এবং তাঁর স্বামী রেগ রায়ান ১৯৬৩ সালে এই ভুতুড়ে জায়গাটি কেনেন। অলিভ বলেন যখন তাঁরা হাজির হন বাড়িটাতে কোন বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকলেও এর বাতিগুলো জ্বলছিল। তাঁরা ভেবেছিলেন চোরেরা এসেছে বাড়িটায় যেসব মূল্যবান জিনিসপত্তর আছে সেগুলো হাতিয়ে নিতে। অলিভ এবং বাচ্চাদের গাড়িতে রেখেই রেগ গেলেন ভেতরে, কী হয়েছে দেখতে। কিন্তু সদর দরজার সামনে হাজির হতেই সব বাতি নিভে গিয়ে অন্ধকারে নিমজ্জিত হলেন। প্রথম দিনের এই ঘটনার পর একের পর এক অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটতে লাগল। ওপরের বারান্দায় প্রায়ই হিল পরা এক নারীর পদশব্দ শুনতে পেতে লাগলেন স্বামী-স্ত্রী। ওই বারান্দাটা তখন ছিল ছোট-বড় গর্তে ভরপুর এবং একেবারেই ব্যবহার অযোগ্য। কারও সাহায্য ছাড়াই জিনিসপত্র নড়াচড়া করে বেড়ায় আজব এই বাড়িতে। শোনা যায় অস্বাভাবিক শব্দ। মাঝে মাঝেই অশুভ একটা অনুভূতি হয় মনে। তবে ১৯৬০-৭০-এর দশকে মানুষের মধ্যে কুসংস্কার ছিল অনেক বেশি। তাই এসব অভিজ্ঞতা আশপাশের লোকদের কাছে তখন বলতেন না পরিবারের সদস্যরা।
ব্রায়ান পরিবার এখন বাড়িটাতে গোস্ট ট্যুর পরিচালনা করেন। রাতে থাকার ব্যবস্থাও আছে। জায়গাটার বেশ কিছু অস্বাভাবিক ছবিও ক্যামেরাবন্দি করতে পেরেছেন তাঁরা।
ধারণা করা হয় মোটমাট এগারোটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটে এখানে। রায়ান পরিবারের সদস্যদের অনুমান এই অস্বাভাবিক মৃত্যুগুলোর কারণেই বাড়িটাতে নানা ধরনের অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটে। আর এভাবে মারা যাওয়া মানুষগুলোর আত্মারাই মুক্তি না পাওয়ায় ঘুরছে বাড়ির সীমানার ভেতরে।
অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের জুনিতে অবস্থিত ভিক্টোরিয়ান ম্যানর ধাঁচের এই বাড়িটি। পঞ্চাশ বছর ধরে এই অদ্ভুতুড়ে বাড়িতে বাস করছেন অলিভ রায়ান। তিনি দাবি করেন বাড়ির আসল মালিক ক্রিস্টোফার এবং এলিজাবেথ ক্রউলির উপস্থিতি এখনও টের পান তিনি। ১৯১০ সালে ক্রিস্টোফার এবং ১৯৩৩ সালে এলিজাবেথ মারা যান। কিন্তু তাতে তাঁদের প্রেতাত্মাদের এই বাড়িতে হানা দেয়া থেমে থাকেনি। ক্রিস্টোফার উইলিয়াম ক্রউলি এই ম্যানর হাউস বানিয়েছিলেন ১৮৮৫ সালে।
একবার শুনলাম ব্যালকনি থেকে কেউ আমার নাম ধরে ডাকছে। ব্যালকনির কাছে আসতেই পদশব্দও শুনলাম। কিন্তু সেখানে পৌঁছে কাউকে পেলাম না। আসলে আমি এবং আমার প্রয়াত স্বামী রেগ এখানে আসার প্রথম দিন থেকেই অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটতে থাকে। সবসময়ই মনে হত কেউ আমাকে দেখছে। আমার ধারণা এ বাড়িতে যেসব দুর্ঘটনা কিংবা অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় সেসবই এসব ভুতুড়ে ঘটনার জন্য দায়ী। একটা ছোট বাচ্চা ন্যানির কোল থেকে সিঁড়িতে পড়ে গড়াতে গড়াতে মারা যায়। সে অবশ্য দাবি করে রায়ান দম্পতি বাচ্চাটাকে তার হাত থেকে অদৃশ্য কিছু একটা ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। এদিকে মি. ক্রউলির কারণে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়া এক চাকরানীও ব্যালকনি থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। কেউ কেউ আবার বলে তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে মারা হয়েছে। তার প্রেতাত্মার দেখা মেলে মাঝে মাঝেই। এদিকে খড়ের গাদায় আগুন লেগে মারা যায় আস্তাবলে কাজ করা একটি ছেলে। ১৯৬১ সালে এখানকার এক কেয়ারটেকারও গুলি খেয়ে মরে। এ বাড়ির এক হাউসকিপার তার উন্মাদ ছেলেকে বাইরের একটা ছাপরায় শিকল দিয়ে বেঁধে রাখে দীর্ঘ ত্রিশ বছর। ওর নাম ছিল হ্যারল্ড স্টিল। চুল না কাটার কারণে চারপাশে নেমে এসে এবং জট বেঁধে বীভৎস হয়ে ওঠে হ্যারল্ডের চেহারা। রাতের বেলা পৈশাচিক কণ্ঠে চিৎকার করত সে। আশপাশের বাড়িগুলোতে বাস করা বাচ্চারা ভাবত একটা দানবকে আটকে রাখা হয়েছে ম্যানসনের ভিতরে। তারা ওর খোঁজে আসত পর্যন্ত। রাতের বেলা এখনও লোকেরা হ্যারন্ডের বুনো চিৎকার আর শিসের শব্দ শুনতে পায়।’ বলেন, অলিভ রায়ান। এক কথায় একটা ভুতুড়ে বাড়ির তকমা গায়ে সাঁটার জন্য যা যা দরকার এর সব উপাদানই মজুত আছে মন্টিক্রিস্টো হাউসে।
অলিভের ছেলে লরেন্স এই বাড়িতে বেড়ে উঠেছে। সে জানায় ছোট বয়স থেকেই বুঝতে পারে বাড়িটাতে সব কিছু স্বাভাবিকভাবে চলছে না। চার বোনের সঙ্গে এখানেই বেড়ে ওঠে সে। ‘বাড়িটা কেনার পর মা-বাবাকে এটার সংস্কারে অনেক টাকা ব্যয় করতে হয়। এটার ছিল বেশ জরাজীর্ণ অবস্থা। আর পরিত্যক্ত অবস্থায় লুটেরারা যা পেরেছে এখান থেকে নিয়ে গিয়েছে। বাবার সবসময় একটু দোতলা বাড়ির স্বপ্ন ছিল। এর মাধ্যমে তা পূরণ হয়। এটা কেনেন এক হাজার ডলারে। এতে তখন ছিল অর্ধেকখানি ধসে পড়া মূল ভবন, ইটের একটা দালান, ভৃত্যদের কোয়ার্টার ও আস্তাবল। বাবা পেশায় ছিলেন একজন দর্জি। রোজগারের জন্য রাত- দিন খাটতেন। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে আমাকে ঘিরে অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা হয় বাড়ির লোকেদের। মা-বাবা বলরুমে একটা পার্টির আয়োজন করেছিলেন। বেশ রাত হয়ে গেলে এক বোন আমাকে বিছানায় পৌঁছে দেয়। একটু পরই বোনদের কেউ না কেউ এসে আমাকে দেখে যাচ্ছিল। আমার সবচেয়ে ছোট বোনের বয়স তখন বারো। যখন আমাকে দেখে যেতে এল, আবিষ্কার করল একজন লোক আমার বিছানার কিনারায় বসে একদৃষ্টিতে দেখছে আমাকে। তারপরই বোনের দিকে ফিরে অশুভ একটা চাহনি দিল। চিৎকার করে দৌড়ে বলরুমে গিয়ে মা-বাবাকে সে জানাল আমার রুমে অদ্ভুত, অচেনা এক লোক বসে আছে। যখন তারা এল লোকটা নেই, আমি দিব্যি ঘুমাচ্ছি। পুরনো দিনের একটা পোশাক পরে ছিল রহস্যময় ওই মানুষটি, জানায় আমার বোন। অনুমান করা হয় ওটা মি. ক্রউলির ভূত। এই ঘটনার পরে আরও কয়েকবার চেহারা দেখিয়েছে সে। আমার বয়স যখন তেরো তখন প্রথম ঘটনাটা জানতে পারি বোনের কাছ থেকে। ওই কামরাটা আমার এখনও অপছন্দ। মনে হয় কেউ যেন আমাকে দেখছে। তবে মি. ক্রউলির চেয়ে বেশি অশুভ আর বিরক্তিকর হলো মিসেস ক্রউলির ভূত। সে লোকজন একেবারেই সহ্য করতে পারে না। কখনও কখনও কোন হতভম্ব পর্যটককে ‘বেরিয়ে যাও’ বলে চমকেও দিয়েছে ভূতটা। মি. ক্রউলি মারা যাওয়ার পরও আরও তেইশ বছর এ বাড়িতে কাটিয়েছিল ভদ্রমহিলা। বেঁচে থাকা অবস্থায় যেমন অতিথি পছন্দ করত না এখনও ওই একই অবস্থা। আঠারো মাসের ছোট্ট মেয়ে মেগডেলেন ক্রউলির ভূত দেখার কথাও বলে কেউ কেউ। আসলে গৃহকর্ত্রী মিসেস ক্রউলি চাকর-বাকর ও কর্মচারীদের সঙ্গে খুব বাজে ব্যবহার করত। ধারণা করা হয় মেগডেলেনকে ওই ন্যানি মেয়েটা ইচ্ছা করে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল সিঁড়ি থেকে। ওই জায়গাটায় গেলেই কোন কারণে সবার মন খারাপ হয়ে যায়।
এটা কি ঘটনাটা আগে থেকে জানা থাকায় নাকি মেয়েটার অতিপ্রাকৃত উপস্থিতির কারণে বলতে পারব না। তবে সেখান থেকে অনেককেই কাঁদতে কাঁদতে বের হতে দেখেছি। আমাদের গোস্ট ট্যুরগুলো পরিচালনা করা হয় মোমের আলোয়। অতিপ্রাকৃত ভ্রমণ শেষে যাঁরা ভৃত্যদের পুরনো কোয়ার্টারে রাত কাটান তাঁদের হয় জীবনের সেরা ঘুমটা হয়, নতুবা ঘুম আসে না একেবারেই। এমনও আছে গোটা রাতটা এখানে কাটানও না কেউ কেউ। গাড়িতে চেপে শহরে চলে যান। আমি একজন প্রফেশনাল স্টান্টম্যান। তবে প্রতি হপ্তায় একবার হলেও বাড়িতে আসি। ভুতুড়ে ঘটনা বাদ দিলে ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনায়ও এটি একটা চমৎকার দালান। মা-বাবা অনেক কষ্ট করে একে আবার পুরনো চেহারা ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাই এই দালানটা নিয়ে আমি গর্বিত। যদিও এখানে এলে ভয়ের একটা অনুভূতি অনেক সময় কাজ করে আমার মধ্যেও।’ এদিকে তার স্ত্রী সোফিয়া এখানে আসার পর অদ্ভুত এক অনুভূতির শিকার হয়। তার মনে হয় এ বাড়িতে আগেও এসেছে সে। একপর্যায়ে অনুভব করে ক্রউলিদের সময় এই বাড়ির একজন পরিচারিকা হিসাবে কাজ করত সে। ওই সময়ের অনেক স্মৃতিই মনে পড়ে তার। কখনও কখনও বাড়ির পুরানো ভৃত্যদের দেখতে পায়। এমনকী মি. ক্রউলির উপস্থিতিও টের পায়। তাই মন্টিক্রিস্টোর সঙ্গে তার সম্পর্ক অনেক গভীর। তবে সত্যি তার পুনর্জন্ম হয়েছে নাকি অন্য কোন শক্তি তাকে এমন ধারণা দিচ্ছে বোঝা মুশকিল। এখন অবশ্য গোস্ট ট্যুরগুলো পরিচালনায় বড় ভূমিকা থাকে সোফিয়ার। ভূত নামাবার মিডিয়াম হিসাবেও কাজ করে।
এই বাড়ি থেকে তোলা কিছু কিছু ছবি আসলেই পিলে চমকে দেবে আপনার। একটা ছবিতে ছায়াময় এক কাঠামোকে একটা ঘোড়ার গাড়ির ওপরে ঝুলে থাকতে দেখা যায়। আরেক ছবিতে আবার রহস্যময় এক হাতের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। অপর এক ছবিতে আয়নাতে দেখা যায় আদিবাসী এক ভৃত্যের ঝাপসা চেহারা। এক পর্যটক পুরানো এক বেডরুমের ছবি তুলেছিলেন। দেখা যায় বাম পাশে ছায়াময় একটা আকৃতি ভাসছে। এই বাড়িতে আসা অনেকেই অতিপ্রাকৃত উপস্থিতি টের পেয়েছেন।
রায়ান পরিবারের পরিচালিত ট্যুরে অনেক পর্যটকই অদৃশ্য কিছু একটা তাঁদের স্পর্শ করেছে দাবি করেছেন। রাতে ঘুমাতে গিয়ে কেউ ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠেন। কেউ আবার শরীরে কোন একটা অদৃশ্য কিছুর ওজন অনুভব করেন।
অবশ্য বিজ্ঞান লেখক ফিলিপ বেল এখানকার রহস্যময় ব্যাপারগুলোর একটা ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন কিছু কিছু শব্দের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এতই কম যে মানুষের কানে পৌছে না। কিন্তু শরীর এটা অনুভব করতে পারে। তখনই নানা ধরনের ভুতুড়ে অনুভূতি হয় তাদের। তবে মি. রায়ান বলেন, এই বাড়িতে একটা ভ্রমণ অবিশ্বাসীদের চিন্তাধারা বদলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। ‘অনেক অবিশ্বাসীই এ বাড়িতে ঢুকেছেন। তবে যখন বেরিয়ে যান, অতিপ্রাকৃত শক্তির উপস্থিতি এবং মৃত্যুর পরের জগৎ সম্পর্কে দ্বিতীয়বার ভাবতে শুরু করেন।’
অদৃশ্য সাহায্যকারী
প্রেতাত্মা সম্পর্কে মানুষের ধারণা অনেকটাই বদলে দিয়েছে কানাডার ল্যাব্রাডরের এক অশরীরী। প্রেত মানুষের ক্ষতি করে এটাই সাধারণ ধারণা। কিন্তু ল্যাব্রাডরের ওই প্রেতাত্মা বিপদে মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসে, তাদের পথ দেখায়।
শুরুতে বরং ফ্রেড কর্কবির কাহিনীটি শোনা যাক। পারট্রিজ হিলের দুর্গম এক পথে চলছিল কৰ্কবি। দশটা কুকুর তার স্লেজ গাড়িটা টেনে নিয়ে চলছিল। হঠাৎ পুব দিক থেকে ধেয়ে এল তুষার ঝড়। চারপাশ ঝাপসা হয়ে গেল। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না কর্কবি। ভেজা স্কার্ফটা দিয়ে ঢেকে মুখ বাঁচানোর চেষ্টা করল। এদিকে ঝড়ে স্লেজটা নিয়ে কুকুরগুলো দিগ্বিদিক্ দৌড়চ্ছে।
তুষারকণাগুলো মুখে বিঁধছে সূচের মত। শীতল বাতাসে চোখ খুলে রাখা মুশকিল। হঠাৎই একটা খাদের কিনারে এসে দাঁড়িয়ে গেল কুকুরেরা। কয়েক পা এগুলেই খাদে পড়ে মৃত্যু হত সবার। পঁয়তাল্লিশোর্ধ্ব শিকারি কর্কবির মনোবল অসাধারণ। এই পরিস্থিতিতেও মাথা ঠাণ্ডা রাখল। বুঝতে পারল পথ হারিয়েছে। তাড়াতাড়ি এখান থেকে সরে না পড়লে খারাপি আছে কপালে। ঝড়ো বাতাসে হয়তো গিয়ে পড়বে খাদে।
এসময়ই জোরে ঘেউ ঘেউ করতে শুরু করল কুকুরগুলো। ছুটে যেতে চাইল। ব্যাপারটা কী বোঝার জন্য স্লেজের কাছে এগিয়ে গেল কর্কবি। এসময় কাছেই আরও কিছু কুকুরের শব্দ কানে এল। ভালভাবে চারপাশে তাকাতেই দেখল তুষারের মধ্যে চোদ্দ-পনেরোটা কুকুর অপর একটি স্লেজ টেনে নিয়ে যাচ্ছে। স্লেজের পেছনে দাঁড়িয়ে সাদা ফারের পোশাক গায়ে চাপানো বিশালদেহী এক লোক। হাতে চাবুক। চিৎকার করে লোকটাকে ডাকল কর্কবি। কিন্তু ঝড়ে হারিয়ে গেল তার কণ্ঠস্বর। লোকটার কোন দিকে খেয়াল নেই, কুকুরগুলোর শরীরে চাবুকের বাড়ি কষাতে কষাতে দ্রুত চলে যাচ্ছে। মনস্থির করে ফেলল কর্কবি। ওদের পেছনেই যাবে। তাছাড়া লোকটার আচরণ দেখে বোঝা যাচ্ছে এই এলাকা হাতের তালুর মতই চেনে। অতএব দেরি না করে
রগুলোকে ছোটাল ওই লোকটা এবং তার স্লেজটানা *সুরগুলোর পেছনে। মোটামুটি এক ঘণ্টাটাক পরে ফ্রেঞ্চম্যান’স আইল্যাণ্ডে সৈনিকদের ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌছে গেল। যে দলটাকে অনুসরণ করছিল একটা বাঁক নিয়ে ওটা কোথায় হারিয়ে গিয়েছে বলতে পারবে না।
একটু পরে গ্রামের একমাত্র সরাইখানাটায় পৌছল। ভেতরে ঢুকে কিছু পান করতে করতে শরীর গরম করতে লাগল আগুনে। এই ফাঁকে সরাইমালিককে জিজ্ঞেস করল, ‘একটু আগে একটা কুকুরের দল নিয়ে আসা ওই লম্বা-চওড়া লোকটাকে চেনো?’
‘কী বললে? তুমিই প্রথম। তোমার আগে অন্য কোন আগন্তুক গ্রামে আসেনি আজ।’
‘ধুর, এটা হয় নাকি? সেই ল্যাব্রাডর থেকে তার পেছন পেছন এসেছি। হাওয়ায় মিলিয়ে যায় কীভাবে?’
‘যার পিছু নিয়ে এসেছ সে মানুষ নয়, অশরীরী। তোমার বিপদ দেখে সাহায্য করেছে। ওর নাম স্মোকার।’
অল্প কিছুদিন হলো কুইবেক থেকে ল্যাব্রাডর এসেছে কর্কবি। মোটেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ নয় সে। কিন্তু কথা বলতেই বুঝতে পারল এখানে স্মোকারকে নিয়ে যেসব গল্পগাথা প্রচলিত সেগুলো একেবারে উড়িয়ে দেয়ার মত নয়। ইজু ডিলিংহ্যামের প্রেতই এখানকার লোকেদের কাছে স্মোকার নামে পরিচিত। তুষার ঝড়ে বিপদে পড়া মানুষদের সাহায্য করে এই উপকারী প্রেতটি.
আশ্চর্য ব্যাপার, কেবল দুর্যোগের সময় দেখা যায় স্মোকারকে। গত অর্ধ শতাব্দী কিংবা এর বেশি সময়ে অসংখ্য শিকারি, অভিযাত্রী তাকে দেখেছে, বিপদে তার সাহায্য পেয়েছে।
কে এই ইজু ডিলিংহ্যাম? তার ব্যবসা ছিল মদ চোলাই করা। গোটা ল্যাব্রাডর এলাকায় তার মদের খ্যাতি ছিল। যারা মদ চোলাই করে তাদের বলে স্মোকার। তাই ইজু ডিলিংহ্যামের প্রেতাত্মার নাম হয়ে যায় স্মোকার। সে কোথা থেকে এসেছে নিশ্চিত করে বলা যায় না। ধারণা করা হয় কুইবেকের গাসপে উপদ্বীপ থেকে ল্যাব্রাডরে এসেছিল শিকার করতে। কেউ আবার বলে সে এসেছিল নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড থেকে। যেখান থেকেই আসুক এই জায়গাটার প্রেমে পড়ে যায়। রাতারাতি, মদের ব্যবসায়ও খ্যাতি পেয়ে যায়। ফলে এখানেই থিতু হয়। ব্রুস গাছের ফল, চিনিসহ নানান জিনিস মিশিয়ে একেবারেই অন্য ধরনের একটা মদ বানাত। গোপন এক জায়গায় ছিল তার ভাটিখানা। ১৯১০ সালে এই অঞ্চলে আসে সে, মারা যায় ১৯২০ সালে। এই দশ বছর মদের ব্যবসাই করে। প্রথম কয়েক বছর দারুণ ব্যবসা করে সে। শীতের সময় স্লেজ গাড়িতে করে মদ নিয়ে নানান জায়গায় বিক্রি করত। গরমে মদ পরিবহনে ব্যবহার করত নৌকা। তারপরই ১৯১৬ সালে ঘটল একটা দুর্ঘটনা। ডিলিংহ্যামের মদগুলো ছিল বেশ কড়া। একবার ওগুলো খেয়ে কয়েকজন মদ্যপ প্রচণ্ড মারামারি করে এবং এতে একজন মারাও যায়। এই ঘটনায় ডিলিংহ্যামেরও এক বছরের কারাদণ্ড হয়। জেল থেকে বেরিয়ে সে জেলারকে বলে তাকে আর কখনও কয়েদখানায় ঢোকাতে পারবে না কেউ।
আবার মদ তৈরিতে মন দিল। এবার শিকারও শুরু করল। তবে সাদা প্রাণীর দিকেই ঝোঁক। তুষারসাদা আর্কটিক শিয়াল ছাড়া অন্য কোন প্রাণী শিকার করত না। ওগুলোর চামড়া দিয়ে সাদা একটা ফারের পোশাক বানাল নিজের জন্য। সাদা এক দল কুকুর জোগাড় করল কোথা থেকে। নতুন স্লেজটার রংও সাদা। বরফে লুকিয়ে পড়তে ভারী সুবিধা হলো এতে। কয়েকবার তাড়া করে বোকা বনল পুলিস।
১৯১৯ সালের ঘটনা। এক গুপ্তচর এসে পুলিসকে বলল স্মোকারের মদের ভাটি আছে ব্রাজিল’স পিঞ্চ বলে একটা জায়গার কাছে জঙ্গলের ভেতর। এদিকে মদ তৈরির উপকরণের খোঁজে স্মোকার তখন এসেছিল ফ্রেঞ্চম্যান’স আইল্যাণ্ডে। তাকে সেখানেই ধরল পুলিস। তার সঙ্গে রফা করার চেষ্টা করল পুলিস। বলল সে যদি তাদের মদের ভাটিখানায় নিয়ে যায় কেবল এক বছরের জেল হবে। না হলে হবে তিন বছর। জবাবে স্মোকার বলল, ‘বেশ তো, জঙ্গলে গিয়ে তবে খুঁজে বের করো আমার ভাটিখানা।’ পুলিস কর্মকর্তাটি এবার কনস্টেবলদের জঙ্গলে গিয়ে ভাটিখানা খুঁজে বের করার নির্দেশ দিলেন। তারা যখন রওয়ানা দেবে এসময় পেছন থেকে ডেকে স্মোকার বলল, ‘আমার ভাটিখানার চারপাশে অন্তত পঞ্চাশটা ভালুক ধরার ফাঁদ আছে। ওগুলো এমনভাবে লতা-পাতা দিয়ে লুকানো, না পড়লে টেরই পাবে না। ভালুক ধরার ফাঁদ যে কতটা ভয়ঙ্কর তা তো জানোই। ওটায় পড়লে পা বাদ দিতে হবে সন্দেহ নেই।’ কনস্টেবলরা ভয় পেল। পা হারালে খাওয়াবে কে? অনেক বকাঝকা করেও তাদের জঙ্গলে পাঠাতে পারলেন না অফিসার। এদিকে স্মোকারের কাছ থেকেও একটি কথাও উদ্ধার করা গেল না। উপায়ান্তর না দেখে তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হলো পুলিস। এরপর আর তার পিছু নেয়নি।
কিন্তু স্মোকার দিনকে দিন আরও বেপরোয়া হয়ে উঠল। এক মহিলাকে অপহরণ করে মুক্তিপণ চাইল আত্মীয়-স্বজনের কাছে। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী অর্থ দিতে ব্যর্থ হলো পরিবারটি। মহিলাকে নিজের সব উগ্র মদ খাইয়ে পাগল বানিয়ে ফেলল সে। ওই অবস্থায় শহরে পাঠিয়ে দিল। দিনকে দিন নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে লাগল স্মোকার। সাদা কুকুর দেখলেই চুরি করে। নিজেও এখন আচ্ছাসে মদ গেলে। একদিন এক আদিবাসীর সঙ্গে জোর লড়াই বাধল তার। একপর্যায়ে লোকটাকে খুন করে পালাল। কেউ যেন তাকে ধরতে না পারে সেজন্য জঙ্গলে পেতে রাখল একের পর এক ভালুক ধরার ফাঁদ।
সব কিছুরই একটা শেষ থাকে। অবশ্য স্মোকারের বেলায় এটাকে শেষ বলা মুশকিল। তবে অন্তত তার খারাপ রূপটির শেষ হলো এর মাধ্যমে। অনেক উঁচু এক মাচায় বসে মাছ ধরছিল নিচের এক খালে। হঠাৎ পা ফস্কে নিচে পড়ে মেরুদণ্ড ভেঙে যায় তার। লোকজন ধরাধরি করে নিয়ে যায় পুলিসের তাঁবুতে। সেখানে বেশ যত্নআত্তি করা হলেও মোটে তিন দিন আর বাঁচল স্মোকার। তবে মারা যাওয়ার আগে খুব অনুশোচনা হয়। বলে তার এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবে কুকুরের পাল নিয়ে মানুষের বিপদে সাহায্য করে। মৃত্যুর পর কবর দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাপা পড়ে যায় তার এই প্রতিজ্ঞাও। লোকে ভুলে যেতে বসে তাকে।
ছ’হপ্তা পরের ঘটনা। এক শিকারি ফ্রেঞ্চম্যান’স আইল্যাণ্ডের দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎ প্রবল তুষার ঝড়ের মধ্যে পড়ে পথ হারায় সে। এসময়ই দেখে সাদা ফারের পোশাক পরা বিশালদেহী এক লোক কুকুরেটানা স্লেজ নিয়ে ছুটছে। তাকে অনুসরণ করে লোকটাও পৌছে যায় নিরাপদ জায়গায়। সরাইখানায় পৌঁছে গা গরম করতে করতে খুলে বলে ঘটনা। কিন্তু সেখানে উপস্থিত সরাইমালিকসহ অন্যরা জানায় আজ আর কেউ ওই দিকে যায়নি। তখনই সবার মনে পড়ে স্মোকারের প্রতিজ্ঞার কথা। তবে তখনও পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছিল না। তারপর যখন একের পর এক শিকারি ওই দীর্ঘকায় সাদা পোশাকের রহস্যময় লোকটির কারণে বৈরী আবহাওয়ায় পথের দিশা পেতে লাগল, তখন আর কারও বুঝতে বাকি রইল না স্মোকার তার কথা রেখেছে।
কত মানুষকে সে বাঁচিয়েছে তার কোন হিসাব নেই। এমনকী জীবিত থাকা অবস্থায় যে পুলিস সদস্যরা ছিল তার দুশমন তাদেরও বাঁচায় স্মোকার। দু’জন পুলিস কর্মকর্তা এমনই এক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। জর্জ বেটসন ও এড রিয়োপল তাঁদের নাম। ১৯৪৯ সাল। এই দুই কর্মকর্তা তুষার ঝড়ে পথ হারান। এসময়ই প্রবল ঝড়ের মধ্যে কুকুরের একটা দলকে স্লেজ টানতে দেখেন। ওটার সঙ্গে আছে সাদা পোশাকের দীর্ঘদেহী এক লোক। দেরি না করে দলটাকে অনুসরণ শুরু করেন তাঁরা। দুই ঘণ্টা ওদের পিছন পিছন যাবার পর দেখেন পুলিসের একটা ক্যাম্পের কাছে চলে এসেছেন। এদিকে ওই কুকুরের দল, স্লেজ এবং লোকটা অদৃশ্য হয়েছে। মজার ঘটনা যে স্মোকার জীবিত থাকা অবস্থায় ছিল মানুষের আতঙ্ক, এমনকী বাচ্চাদের ভয় দেখাতেও ব্যবহার করা হত তার নাম, মারা গিয়ে সে হয়ে গেল উপকারী এক প্রেতাত্মা। লোকেরা বলে স্মোকারের দেখা পেয়েছ মানে তুমি বেঁচে গেছ। সে তোমাকে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে না দিয়ে যাবে না।
পিটার অ্যানডোনি ছিলেন বুড়ো এক শিকারি। স্মোকার সম্পর্কে তাঁর বিস্তর জ্ঞান। তাঁর কথা হলো, ‘ঝড়ের সময় খুব বিপদে পড়েছ, এসময় তোমার কুকুরগুলো যদি হঠাৎ চিৎকার করতে শুরু করে বুঝবে স্মোকার ধারেকাছেই আছে। তাকে খুঁজে বের করে অনুসরণ করো, ব্যস, তোমার আর কোন সমস্যা হবে না। এ পর্যন্ত হাজারের বেশি মানুষকে বাঁচিয়েছে এই ভাল প্রেত।
অ্যান্ড্রু এসেছিল
স্কুল ও কলেজগুলোতেও নানা ধরনের ভূতের খবর পাওয়া যায়। এবারের ঘটনাটি ইংল্যাণ্ডের চ্যারিং ক্রস থেকে দুই মাইল দূরের বিখ্যাত বি. স্কুলের। বর্ণনাকারী মার্টিন ফ্ল্যামারিকের মুখ থেকেই বরং এটা শুনি।
১৮৭০-এর আগস্টের এক সন্ধ্যা। স্লোয়েইন রোডে হঠাৎই বি. স্কুলের পুরানো বন্ধু জ্যাক অ্যাণ্ডুর সঙ্গে দেখা। বহু বছর তার সঙ্গে দেখা নেই। সঙ্গে এক মহিলা। দীর্ঘদেহী, চোখা চেহারার এই নারী নিঃসন্দেহে বিদেশী। এতটাই সুন্দরী যে চেহারা থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারছিলাম না।
‘আমি দুঃখিত, গল্প করার জন্য দাঁড়াতে পারছি না,’ বলল অ্যান্ড্রু। ‘তাড়া আছে খুব। রাতেই স্পেনের বার্সেলোনার উদ্দেশে ইংল্যাণ্ড ছাড়ছি। এখন ওখানেই থাকি। ‘অ্যাংলো- বার্সেলোনিয়ান’ নামের একটা ইংরেজি পত্রিকায় চাকরি করি। ডিসেম্বরে স্কুলের অনুষ্ঠানে আসছ তো?’
জানালাম, ইতোমধ্যে প্রধান শিক্ষককে আমার উপস্থিত থাকার বিষয়টা নিশ্চিত করেছি।
‘তাহলে ভালই হলো। আমিও থাকব। হাউস সাপারে একটা বক্তব্যও দেয়ার কথা আমার। বড়দিনে স্পেনে থাকার ইচ্ছা নেই আমাদের। ইংল্যাণ্ডেই বন্ধু ও আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সময়টা কাটাব। তখন তোমার সঙ্গে দেখা হবার অপেক্ষায় থাকলাম। অনেক কিছু বলার আছে। এখন কেন দাঁড়াতে পারছি না আশা করি বুঝতে পারছ। গুড লাক, বন্ধু।’ এই বলে চলে গেল তারা। ঘুরে তাকিয়ে ভিক্টোরিয়ার একটা বাসে উঠতে দেখলাম। অ্যাণ্ডুর সঙ্গে দেখা হয়ে সত্যি খুব ভাল লাগছিল। কারণ আমার বি. স্কুলের ঘনিষ্ঠ দোস্তদের একজন ছিল সে। এক ক্লাসে একই সঙ্গে ভর্তি হই। স্কুল ছাড়ার পর মাঝখানের দীর্ঘ সময়ে একবার ছাড়া দু’জনের আর দেখাই হয়নি।
সে মেয়েটার সঙ্গে কেন পরিচয় করিয়ে দিল না এটা ভেবে অবাক লাগল। তবে এটাও ঠিক তাদের খুব তাড়া ছিল। নিঃসন্দেহে নারীটি তার স্ত্রী। সৌভাগ্য আর কাকে বলে! এত সুন্দরী একটা বউ পেয়েছে। চোখা চেহারা, রসালো ঠোঁট, টানা টানা চোখ, লম্বা পা। উঁচু হিল পরে ছিল। মোজার ফুটো দিয়ে গোলাপী পা দেখতে পাচ্ছিলাম। আবার ভাবলাম, হয়তো তার বোন। তাহলে আমার একটা সুযোগ তৈরি হয়। হয়তো আমাকে বার্সেলোনায় তাদের বাড়িতে যাওয়ার দাওয়াতও দেবে। বার্সেলোনা নিয়ে রীতিমত পড়াশোনা শুরু করে দিলাম। জ্যাককে লম্বা-চওড়া একটা চিঠিও পাঠালাম। তবে বন্ধুর চিঠি পেয়ে কিছুটা দমে গেলাম। ওই মহিলা কিংবা বাড়িতে দাওয়াতের ব্যাপারে কিছু বলেনি। স্কুলের পুরানো দিনের কথা বারবার লিখেছে। অনুষ্ঠানটার ব্যাপারে তার বেজায় আগ্রহ, কোথায় আমাদের দেখা হবে এসব বিষয়ে লিখেছে। এভাবে কয়েকবার চিঠি চালাচালি হলো। শেষবার তার চিঠি পেলাম নভেম্বরের ২৫ তারিখ। তারপর আর কোন খবর পেলাম না। ডিসেম্বরের ১০ তারিখ ইংল্যাণ্ডের জাহাজে চেপে বসার কথা।
শেষ পর্যন্ত এল ঘটনাবহুল সেই সন্ধ্যা। একটা বক্তব্য দেয়ার কথা আমারও। বক্তা হিসাবে আমি একেবারেই গড়পড়তা ধরনের। তাছাড়া বড়দের সামনে বলা এক জিনিস আর স্কুলের ছেলেদের সামনে বলা আরেক কথা। শুরুর অনুষ্ঠানে অন্তত হাজারখানেক পুরানো ছাত্র উপস্থিত ছিল নতুনদের পাশাপাশি। স্কুলের সঙ্গীতটা যখন হলো মনে হচ্ছিল যেন শব্দে কানে তালা লেগে যাবে। ছাত্ররা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গেল হাউস সাপারের জন্য। স্কুল-দালানের প্রবেশ পথে অ্যাণ্ডুর আমার সঙ্গে দেখা করার কথা। ‘গানের সময় সম্ভবত উপস্থিত থাকতে পারব না, তবে স্কুলের পুরনো দালানটার সামনে সাড়ে নয়টার দিকে হাজির হতে ভুল হবে না।’ বলেছিল সে।
কিন্তু জ্যাকের কোন দেখা নেই। একই সঙ্গে হতাশ ও ক্রুদ্ধ হলাম। কেন এল না? আমার সঙ্গে কি তবে মজা করল? প্রধান শিক্ষক সি. গ্রের সঙ্গে কথা বললাম। তিনি বললেন অ্যাণ্ডুর একটা বক্তব্যও দেয়ার কথা। আসবে না, এমন কিছুও জানায়নি। নিশ্চিতভাবেই ভোজের আগেই হাজির হয়ে যাবে। এই আশা নিয়ে অন্য অতিথিদের সঙ্গে হলে প্রবেশ করলাম। সেখানে বয়সে বেশ কয়েক বছরের ছোট দু’জন প্রাক্তন ছাত্রের মাঝখানে নিজেকে আবিষ্কার করলাম। খাবারটাও খুব একটা পছন্দ হলো না। খাওয়া শেষে একটার পর একটা মিনিট পেরোতে লাগল এবং আরও বেশি করে অধৈর্য হয়ে উঠতে লাগলাম। জ্যাকের জন্য রীতিমত উদগ্রীব হয়ে উঠেছি। হঠাৎই মনে হলো মাঝখানের বিশটা বছর যেন এক লহমায় নেই হয়ে গেছে। সত্যি আমি যেন এখনও স্কুলে পড়া সেই ছেলেটি, বালক মনের সেই উত্তেজনা, ভয় সব কিছুই অনুভব করতে পারছি। আমার বাম পাশে তিনটা সিট পরে জ্যাকের আসন। কিন্তু জায়গাটি ফাঁকা, জ্যাক আসেনি। সে শেষপর্যন্ত আমাদের বোকা বানিয়েছে। চেয়ারে পিঠটা এলিয়ে দিয়ে, ভাগ্যকে অভিসম্পাত দিলাম। হঠাৎ শরীরে শীতল একটা অনুভূতি ঘুরে তাকাতে বাধ্য করল আমাকে। দেখলাম, লাজুক জ্যাক কোন্ ফাঁকে তার আসনে এসে বসে আছে।
এটাকে কল্পনা ভেবে, চোখ বন্ধ করলাম। যখন চোখ খুললাম দেখলাম, জ্যাক এখনও সেখানে আছে।
‘জ্যাক!’ সামনে ঝুঁকে ফিসফিস করে বললাম, ওর মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করলাম, ‘জ্যাক!’
তবে অ্যান্ড্রু জবাব দিল না। মনে হচ্ছে শুনতে পায়নি। সিটে চুপচাপ বসে আছে। কনুইদুটো টেবিলের ওপর। চোখ নিচের দিকে। ছোটবেলাতেও এভাবেই বসে থাকত, মনে পড়ল। এসময়ই আমার পাশের একজন জানতে চাইল আমি কী চাচ্ছি? মি. অ্যাণ্ডুর কাঁধে টোকা দিতে বললাম। সে আমার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকাল। ‘মি. ফ্ল্যামারিক, স্কুলবেলা থেকেই কি এরকম মস্করা করতে পছন্দ করো?’
জবাব দিতে যাব এসময় হাউস-শিক্ষক বক্তব্য শুরু করার ঘোষণা দিলেন। আমার এবং জ্যাক দু’জনেরই কথা বলার কথা। এসময়ই আমাকে চমকে দিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন, জে. এল. অ্যান্ড্রু দুর্ভাগ্যজনকভাবে উপস্থিত হতে না পারায় তার বদলে অন্য একজন প্রাক্তন ছাত্র বক্তব্য দেবেন।
‘জ্যাক এখানে নেই!’ নিজেকেই প্রশ্ন করলাম। ‘হয় হাউস-শিক্ষক পাগল হয়ে গিয়েছেন, নতুবা আমি। তাকে এত পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি কীভাবে তাহলে?’ এসব যখন ভাবছি তখনই আমার বন্ধুর চেহারাটা ঝাপসা হতে হতে মিলিয়ে গেল। হাউস-শিক্ষকই ঠিক তাহলে। জ্যাক এখানে নেই।
ওই সময়ই শরীরের শীতল অনুভূতিটার কথা মনে হলো। নিশ্চিত হয়ে গেলাম মোটেই ভুল দেখিনি, কোন ধরনের আত্মার কারসাজি ব্যাপারটা। যা হোক, আমার সময় হলে বক্তব্য দিলাম। তবে জ্যাকের চেহারাটা তাড়া করে বেড়ানোয় মনোযোগ দেয়া কঠিন হচ্ছিল। রাতে যখন বিছানায় গেলাম তখনও ওর কথা ভুলতে পারছিলাম না।
‘এটা খুব অদ্ভুত! অ্যান্ড্রু আমাদের বিষয়টি জানালই না, ‘ পরদিন হাউস-শিক্ষক বললেন, ‘তার কাছ থেকে বিষয়টা ব্যাখ্যা করে একটা চিঠি আশা করেছিলাম। কিন্তু কিছুই আসেনি। হয়তো সে তোমাকে লিখবে। কী হয়েছে জানাতে ভুলো না।’ তাঁকে কথা দিয়ে আর কাউকে বিদায় জানানোর জন্য অপেক্ষা না করে রেলস্টেশনের দিকে রওয়ানা হলাম।
ব্রুক স্ট্রিট, আমার খাস কামরা। অন্য দিনের থেকে তাড়াতাড়িই আজ বিছানায় গেলাম। একপর্যায়ে গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম। পাশের গির্জার ঘড়িতে দুটো বাজার ঘণ্টা বাজতেই হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। মনে হলো যেন ভারী একটা কিছু আছে বিছানায়। হাত বাড়াতেই আতঙ্কিত হয়ে আবিষ্কার করলাম একটা মাথায় পড়েছে হাতটা। চুল থেকে চুইয়ে পানি পড়ছে। এতটাই ভয় পেলাম যে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। এভাবে কতক্ষণ কাটিয়েছি বলতে পারব না। হঠাৎ বুঝতে পারলাম ভারী ওজনটা আর বিছানায় নেই। ওটা বিদায় নিয়েছে। কেন যেন মনে হলো এই ভৌতিক ঘটনার সঙ্গে স্কুলের ওই ঘটনার সম্পর্ক আছে। অ্যাণ্ডুর কি তবে কিছু হয়েছে? বার্সেলোনায় যেতে হবে আমাকে, স্থির করে ফেললাম।
সকালে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটা জিনিস নিয়ে ভিক্টোরিয়ার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। কয়েকদিন পরের এক সন্ধ্যায় পৌছলাম বার্সেলোনা। হোটেলে জিনিসপত্তর রেখে জ্যাক যে পত্রিকা অফিসে কাজ করে সেখানে গেলাম। তবে আমাকে মোটেই সাদর অভ্যর্থনা জানাল না তারা। বলল অ্যান্ড্রু আর এখানকার স্টাফ নয়, তার ঠিকানাও জানা নেই তাদের। আর জানা থাকলেও তাতে আমার কোন লাভ হবে না। তাদের চেহারায় অদ্ভুত এক হাসি খেলা করতে দেখলাম।
মনে হলো জ্যাককে ঘিরে একটা রহস্য দানা বাঁধছে। হয়তো পত্রিকার লোকেরা ওর সম্পর্কে কিছু জানে, কিন্তু বলতে চাইছে না। তারপর গেলাম আমাদের দূতাবাসে। ওটা বন্ধ, কাল এগারোটার আগে খুলবে না। হাতে এখনও কয়েক ঘণ্টা সময় আছে। কী করব বুঝতে না পেরে রাস্তায় রাস্তায় হাঁটতে লাগলাম। একপর্যায়ে একটা মার্কেটের মাঝখানের চত্বরের সামনে চলে এলাম। কয়েকটা গ্যাস ল্যাম্পের আলোয় আঁধার খুব কমই দূর হচ্ছে। চতুর্ভুজাকৃতির জায়গাটা খোয়া দিয়ে বাঁধানো। ইংল্যাণ্ডে এ ধরনের চত্বর আরও অনেক দেখেছি। বেশ অন্ধকার নেমে এসেছে ইতোমধ্যে। বিকালের দিকে শহরের ওপর ঝুলে থাকা ভারী কুয়াশা এখন ভারী বৃষ্টি হয়ে নেমে এসেছে। দ্রুতই রাস্তাঘাট ফাঁকা হয়ে গেল। আমি হোটেলে ফিরে যাওয়ার জন্য ঘুরব, এসময় মৃদু একটা গোঙানির মত শুনলাম মনে হলো। পাকা চত্বরটির মাঝখান থেকে আসছে শব্দটা। কাউকে কি খুন করা হচ্ছে? নাকি এটা আমার জন্য একটা ফাঁদ! আবারও গোঙানির শব্দ শুনলাম। নিশ্চিতভাবেই কেউ খুব যন্ত্রণায় এমন শব্দ করছে, আমার ভেতরের সমস্ত দ্বিধা চলে গেল।
রিভলভারটা হাতে নিয়ে পিচ্ছিল পাথরের ওপর দিয়ে নিঃশব্দে শব্দ লক্ষ্য করে এগুতে লাগলাম। বৃষ্টি ও আলোর স্বল্পতা হেতু সামনে কয়েক ফুটের বেশি দৃষ্টি যাচ্ছে না। পথে কোন ধরনের বাধা থাকতে পারে এটা ভাবিনি। হঠাৎ কাঠের একটা মঞ্চের মত জায়গায় হোঁচট খেলাম। এটার ওপরে উঠব নাকি পাশ কাটিয়ে যাব ভাবছি, এসময়ই দেখলাম আমার কাছেই একটা চৌকির ওপর একটা লোক বসে আছে। বয়স খুব বেশি নয়, পরনে কালো একটা স্যুট। মুখটা হাত দিয়ে ঢাকা থাকায় চেহারা দেখতে পাচ্ছি না। মাথায় টুপি নেই। উন্মুক্ত মাথায় অনবরত বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। তারপর গড়িয়ে পড়ছে শরীর বেয়ে নিচে।
বাহুতে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, এমন বৈরী রাতে এখানে বসে কী করছে। সে কি অসুস্থ? আমি কি তার জন্য কিছু করতে পারি? জবাবে ভয়ানকভাবে গুঙিয়ে উঠল লোকটা। ধীরে ধীরে মুখ তুলল। ওহ্, খোদা, এ তো জ্যাক। এতটাই বিস্মিত যে কথা বলার ভাষাও হারিয়ে ফেললাম। কেবল অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে রইলাম।
‘জমে গিয়েছি প্রায়,’ বিড়বিড় করে বলল সে, ‘চার রাত ধরে এখানে বসে আছি।’
‘চার রাত,’ বিস্মিত কণ্ঠে প্রতিধ্বনি তুললাম, ‘হায়, ঈশ্বর! তুমি উন্মাদ হয়ে গেছ, জ্যাক!’.
মাথা ঝাঁকাল সে। সেখান থেকে পানি টপ টপ করে পড়ল আমার কাপড়ে।
‘না,’ বলল সে, ‘আমি পাগল হইনি। এখানেই আছি।’ তারপর নিজের দিকে একবার তাকিয়ে যোগ করল, ‘তোমাকে বলে কোন লাভ নেই। বুঝবে না।’
‘আমাদের শেষবার দেখা হবার পর নিঃসন্দেহে অস্বাভাবিক কিছু ঘটেছে,’ মত প্রকাশ করলাম, ‘একটা মোটামুটি মাথা গোঁজার মত জায়গায় পৌঁছার পরে আশা করি গোটা বিষয়টা বুঝিয়ে বলবে। আমার ধারণা কোন ধরনের মানসিক যন্ত্রণা এবং বৃষ্টিতে ভেজা এই দুইয়ে মিলে তোমার মাথাটা গেছে। এখন বাড়ি গিয়ে এক বোতল হুইস্কি সাবাড় করা উচিত তোমার।’
‘না,’ ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, ‘ওখানে আর কখনও যেতে চাই না। বরং তোমার আস্তানায় নিয়ে চলো।’
কী করা যায় বুঝতে না পেরে রাজি হলাম। খুব দ্রুতই শর্টকাটে আমাকে হোটেলের কাছে নিয়ে এল সে। অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকাল হোটেলের মালকিন মহিলা। আমার বন্ধুটির মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা মহিলাটিকে একই সঙ্গে ভীত করেছে এবং চমকে দিয়েছে। অবশ্য আমি খুব একটা বিস্মিত হলাম না এতে। কারণ জ্যাকের গাল অস্বাভাবিক রকম সাদা, চুল ভেজা, চোখ অস্বাভাবিক বড় এবং কেমন যেন রক্তাভ হয়ে আছে। সাপার রুমে আমরা ঢুকতেই অন্য অতিথিরা দূরে সরে গেল। ফলে বড় একটা টেবিল শুধু দু’জনের জন্য দখলে পেতে কোন অসুবিধা হলো না। চমৎকার স্বাদের খাবার পরিবেশন করা হলো। ঠাণ্ডা রোস্ট চিকেন, সালাদ, মিষ্টান্ন, কমলার জুস এবং ওপরতোর বিখ্যাত ওয়াইন। আমি রীতিমত খাদকের মত খেলাম। তবে জ্যাক একটা কিছু স্পর্শ করল না।
হতাশার দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালাম। ও যে পাগল হয়ে গেছে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই আমার। ‘তোমার ব্যাপার- স্যাপার বুঝতে পারছি না মোটেই। কয়েকদিন ধরেই কিছু খাচ্ছ না নাকি?’ জানতে চাইলাম।
‘সোমবার থেকে,’ জবাব দিল জ্যাক, ‘আজ শুক্রবার। সোমবার সকালে পাউরুটি আর কোকো খেয়েছি।’
তারপর স্কুলজীবনের গল্প করতে লাগলাম। তবে তার এখনকার জীবন, এখনকার বাড়ি, আর ওই সুন্দরী নারী যাকে জ্যাকের স্ত্রী ভেবেছি, এগুলো সম্পর্কে কিছুই বলল না।
বেশ খরচ হলেও ওর জন্য একটা কামরার ব্যবস্থা করলাম। সেখানে বেশ রাত পর্যন্ত গল্প করলাম।
‘ঠিক আছে,’ ঘড়ির কাঁটা দুটোয় পৌঁছলে অবশেষে বলল সে, ‘বুড়ো বন্ধু, এবার যাও, আমাকে এখানে রেখে। সকালে হয়তো এখনকার আমার সঙ্গে একটু পার্থক্য চোখে পড়বে। তবে যা-ই ঘটুক, আর তোমাকে লোকেরা যা-ই বলুক, সত্য অনুসন্ধানের চেষ্টা কোরো।
কথা শেষ করে শরীরটা বিছানায় এলিয়ে দিল। হতবুদ্ধি অবস্থায় কামরা থেকে বেরিয়ে এলাম। পরের দিন সকালে কী অবস্থায় তাকে পাব এ ব্যাপারে কোন ধারণাই নেই আমার। তবে যে কোন কিছুর জন্যই মানসিকভাবে প্রস্তুত আমি। তবে পরে যেটা জানতে পারি সেটা ছিল আমার জন্য বড় এক ধাক্কা।
সকালে জ্যাকের কামরায় গিয়ে দেখলাম রাতে যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিলাম সে অবস্থাতেই আছে বিছানায়। মাথাটা একটু দরজার দিকে ঘোরানো। হালকাভাবে স্পর্শ করলাম তাকে। কিন্তু কোন সাড়াশব্দ পেলাম না। কপাল ছুঁলাম। বরফের মত ঠাণ্ডা। মাথাটা ধরতেই এক পাশে হেলে পড়ল নিষ্প্রাণভাবে। কোটের কলার সরাতেই গলাটা উন্মুক্ত হলো। ওটা নীল, ফোলা আর…। আতঙ্কে চিৎকার করে উঠে কামরা থেকে ছুট লাগালাম।
একজন চিকিৎসক ডাকা হলো।
ডাকা হলো। তাকেসহ বন্ধুর শয্যাপাশে এলাম। মৃতদেহটা দেখেই ভয় আর বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল। তারপর মৃতদেহের দিকে আঙুল দিয়ে ইশারা করে বলল, ‘ঈশ্বর! সে এখানে কীভাবে এল? জ্যাক অ্যান্ড্রু, খুনিটা, সোমবার সকালে জনসমক্ষে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে! এ কী করে সম্ভব!’
এই ঘটনার পর বেশ কয়েকদিন অসুস্থ হয়ে বিছানায় কাটালাম। মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে জনের শেষ শব্দ কয়টা, ‘সত্য অনুসন্ধানের চেষ্টা কোরো!’
সুস্থ হয়েই খোঁজ-খবর শুরু করলাম। যাকে হত্যার অভিযোগে জনের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে তার নাম কারলোটা গডিভেজ, যে মহিলার সঙ্গে সে বাস করত। লণ্ডনে জ্যাকের সঙ্গে যে সুন্দরীটি ছিল এ-ই সে বুঝতে সমস্যা হলো না আমার।
জ্যাকের সঙ্গে যখন প্রথম দেখা হয় তখন কারলোটা ছিল বিবাহিত। স্বামী হারমান গডিভেজের সঙ্গে থাকত কার্টাজেনায়। জ্যাকের প্রেমে পড়ে তার সঙ্গে পালায় নারীটি। তবে প্রতিবেশীরা নিয়মিতই প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে ঝগড়ার শব্দ শুনতে পেতেন। যখন কারলোটাকে তার সাজঘরে হার্টে ছুরিবিদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায় স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ গিয়ে পড়ে অ্যান্ড্রুর ওপর।
ইংরেজ রাষ্ট্রদূত তখন এখানে ছিলেন না। তাঁর বদলে দায়িত্ব পালন করছিলেন একজন স্পেনীয়। তাছাড়া তথ্য- প্রমাণ ছিল জ্যাকের বিরুদ্ধে। একে বিদেশী, তাতে আবার তেমন ক্ষমতা নেই। তাছাড়া একজনকে বলির পাঁঠা বানানোর দরকার ছিল পুলিসের। অতএব মরতে হলো জ্যাককে।
যা হোক, আমি কার্টাজেনা গিয়ে একজন গোয়েন্দা নিয়োগ করলাম হারমান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য। তার বিরুদ্ধে বেশ কিছু প্রমাণও মিলল। কিন্তু স্পেনীয় পুলিস কোন ব্যবস্থাই নিল না। স্পেনের আইন-কানুনের এই হতাশাজনক অবস্থা দেখে লণ্ডনে ফিরে এলাম। তবে জ্যাকের ব্যাপারে মুখ খুললাম না এখানে। এমনকী আমাদের স্কুলের বন্ধুরা এখনও জানে না জ্যাকের ভাগ্যে কী হয়েছে। তবে স্কুলে এখনও ওর ভূত দেখা যায়, যেমন দেখা যায় যে হোটেলে আমি ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম সেখানে।
কালো মৃত্যুদূত
অশুভ কালো কুকুর নিয়ে এর আগেও টুকটাক লিখেছি। এবারের অধ্যায়টি মূলত এ বিষয়ে গবেষণা করা জে. ওয়েন্টওয়র্থ ডের লেখার রূপান্তর। এখানে এ বিষয়ে আগ্রহী আরও একজন নারীর অভিজ্ঞতা এবং সংগ্রহ করা নানান ঘটনার বিবরণ তুলে ধরেছেন ওয়েন্টওয়র্থ।
উইকেন ফ্যানের জলার ওপরের আকাশে চাঁদ উঠেছে। লাল, গোলাকার। এখানকার জলাভূমি, ডোবা, নলখাগড়ার বন সব আছে সেই হাজার বছর আগের মতই। এর ধারেই একটা সরাইখানায় বসে আগুন পোহাচ্ছে কিছু মানুষ।
‘জলার তীর ধরে যাব আমি। মূল রাস্তা দিয়ে যাওয়ার চেয়ে এভাবে গেলে অন্তত এক মাইল পথ বেঁচে যাবে।’ আমার সিদ্ধান্ত জানালাম।
‘ওই জলা এলাকায় রাতে কালো শয়তান ছুটে বেড়ায়, স্যর।’ মুখে ঢুকে পড়া আগুনের সাদা ছাই থু করে ফেলে বলল জ্যাক বার্টন, ‘ওই পথে যাব না আমি। অনেক টাকার লোভ দেখালেও না।’
‘কারোরই যাওয়া উচিত নয়,’ সুর মেলাল উপস্থিত কয়েকজন, ‘এক মহিলার কী হয়েছিল মনে করতে পারছ, জ্যাক? ওই কুকুরটা তার কাছে এসেছিল রাতে। কয়দিন পরেই মারা যায় সে।’
‘ঠিক আছে, আমি যাচ্ছি,’ বলে ফ্রেডের দিকে ফিরে জানতে চাইলাম, ‘যাবে তুমি? আমার পথেই পড়ে তোমার বাড়ি। বেশ কতকটা সময় বেঁচে যাবে তোমার।’
ঘোড়ার মত ত্রাহিস্বরে চেঁচিয়ে উঠল ফ্রেড, ‘না, স্যর, না, স্যর। কেউ আমাকে রাতে ওই জলার তীর ধরে নিতে পারবে না। এমনকী ইংল্যাণ্ডের রাজাও নয়। তোমার কাছে হাঁস মারার একটা বন্দুক আছে জানি, এর বদলে যদি মেশিন গান থাকত তবুও নয়। যদি যাও, কুকুরটা তোমারও বারোটা বাজাবে।’
একেবারে ছোটবেলা থেকেই ফ্রেডকে চিনি। জলা এলাকায় আমার শিকারের দিনগুলোতে সে ছিল একেবারে যাকে বলে নিয়মিত সহচর। কোন পরিস্থিতিতেই পিছু হটতে দেখিনি তাকে। কিন্তু আজ রাতে সে ভয় পেয়ে গিয়েছে। এমনকী স্বীকারও করছে তা।
‘তুমি কেন এত ভয় পাচ্ছ, ফ্রেড?’
‘বলেছিই তো, ওই কালো কুকুরটা। ওটা এই জলার তীর ধরে রাতের বেলা ঘুরে বেড়ায়। মাস্টার ওয়েন্টওয়র্থ, ওটা আলকাতরার মত কালো, বাছুরের সমান বড়। চোখজোড়া গাড়ির হেডলাইটের মত। তোমার দিকে একবার দৃষ্টি দিলেই হয়েছে, প্রাণে বাঁচবে না।’
‘কিন্তু, ফ্রেড, বুনো হাঁসের পেছনে এখানে রাতের পর রাত ঘুরে বেড়িয়েছে বাবা। তাঁর তো কিছু হয়নি।’
‘স্বীকার করছি, তিনি তা করেছেন। তবে তাঁর ভাগ্য ভাল অশুভ কালো কুকুর তাঁকে চেহারা দেখায়নি, যদি দেখাত তবে তিনি মারা পড়তেন।’
ফ্রেড বলল কয়েক বছর আগে তার বোন এই এলাকায় এক চন্দ্রালোকিত রাতে দেখা করতে আসে তার প্রেমিকের সঙ্গে। তখন কালো কুকুরটার মুখোমুখি হয়ে যায়।
‘স্যর, কুকুরটা তীর ধরে চুপিসারে এগিয়ে আসে ছায়ার মত। ওটার মাথা ছিল নিচের দিকে। যখন আমার বোনের থেকে বিশ গজ দূরে মাথা উঁচু করে তার দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকাল, চোখজোড়া ছিল রক্তের মত লাল। আমার বোনের আত্মা শুকিয়ে যায়। ঘুরে জলার তীর ঘেঁষে উল্টো দিকে দৌড়তে শুরু করে। প্রেমিকের সঙ্গে যখন দেখা হলো তার গায়ে ঢলে পড়ল জ্ঞান হারিয়ে।’ .
‘তার প্রেমিক কি কিছু দেখেছিল, ফ্রেড?’
‘না, স্যর।’
‘কিন্তু তোমার বোন যদ্দূর জানি এখনও বেঁচে আছে। অশুভ জিনিসটা তাকে মারতে পারেনি। আমাদেরও পারবে না।
‘আমার বোনকে তুমি দেখেছ, ওর মত শক্ত মেয়ে আর হয় না, স্যর। তারপরও এক হপ্তা বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেনি। স্বাস্থ্যও ভেঙে পড়েছিল।’
অতএব ফ্রেড আমার সঙ্গে ওই জলা এলাকাটা পার হলো না। সঙ্গে বন্দুক এমনকী এক কোয়ার্ট (প্রায় এক লিটার) বিয়ারের লোভ দেখিয়েও সে রাতে কারও ভয় জয় করতে পারিনি। যখন পরদিন সকালে ফ্রেডকে বললাম ওই রাতে একাই বহাল তবিয়তে জলাভূমির তীর ধরে বাড়ি ফিরে এসেছি, তখন সে উত্তর দিল, ‘তোমাদের মত পুরনো রাজ বংশের মানুষদের কালো কুকুর কখনও কখনও একটু ছাড় দেয় বৈকি।’
ভুতুড়ে এক কুকুরের কিংবদন্তি গ্রেট ব্রিটেনের পুব অংশে ডালপালা মেলেছে বহু বছর ধরে। আমার খুব ঘনিষ্ঠ বান্ধবী লেডি ওয়ালসিংহ্যাম এর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন। এমনকী এর দেখাও পেয়েছিলেন!
এক রাতে সাফোকের লিস্টনে তখনকার লেডি রেনডলশ্যামের সঙ্গে একটা গির্জার গোরস্থানের কাছে বসে ছিলেন। উদ্দেশ্য অশুভ কালো কুকুরের দেখা পাওয়া। আনুমানিক বারোটার দিকে, সমাধিফলকগুলোর মাঝখান থেকে একটা বিশাল কালো ছায়া বেরিয়ে এল, তারপর এক লাফে গির্জার নিচু সীমানা দেয়াল পেরিয়ে বালুর টিলাগুলোর দিকে রওয়ানা হলো। এই দুই নারীর কেউই কুসংস্কারাচ্ছন্ন কিংবা মাতাল ছিলেন না।
নরফোকের ব্ল্যাক শাক নামে পরিচিত কিংবদন্তির সেই কালো ভুতুড়ে কুকুরই আমাদের এই কালো শয়তান। বলা হয় নরফোকের ওই শয়তান কুকুর ক্রোমার এবং শ্যারিংহ্যামের মাঝখানের পাহাড়ি পথ ধরে নিঃশব্দে চলাফেরা করে। এখানকার বাসিন্দাদেরকে এমনকী দশ পাউণ্ড এবং এক বোতল বিয়ারের লোভ দেখালেও তারা রাতে এই পাকদণ্ডী পথে চলতে রাজি হবে না।
ডব্লিউ. এ. ডাট তাঁর দ্য নরফোক ব্রডল্যাণ্ড বইয়ে লিখেছেন, ‘নরফোকের সবচেয়ে ভয়ানক প্রেত বলা চলে ব্ল্যাক শাককে। অ্যাংলো-স্যাক্সন শব্দ স্কাক্কা বা সিয়োক্কা থেকে এসেছে এই শাক শব্দটি। অর্থ শয়তান। এই পৈশাচিক কুকুর গায়ে-গতরে বড় আকারের একটা বাছুরের সমান, ঝোপঝাড়ের ছায়া ধরে নিঃশব্দে চলাফেরা করে সে। একা চলা পথচারীদের অনুসরণ করে, হলুদ চোখের ভয়ানক দৃষ্টি দিয়ে তাদের আঁতকে দেয়। এর সঙ্গে দেখা হওয়া মানে এক বছরের মধ্যে হতভাগ্য লোকটির মৃত্যু। বার্টন ব্রডের কাছের নিটিসহেড লেন তার হানা দেয়ার পছন্দের এক জায়গা। তবে কলটিশাল ব্রিজও তালিকায় ওপরের দিকেই থাকে। ওটার ওপর দিয়ে প্রায়ই মুণ্ডুবিহীন অবস্থায় চলাফেরা করতে দেখা যায় তাকে।’
তবে এই ভুতুড়ে কুকুরের এক অদ্ভুত সংস্করণ নাকি ক্যাম্ব্রিজশায়ারের কাছে সাফোক সীমান্তের সুঘ হিল লেনে ঘুরে বেড়ায়। ক্যাম্ব্রিজের প্যান্টন স্ট্রিটের পুলিস কনস্টেবল এ. টেইলর আমাকে বলেছিল তার যৌবনকালে ওয়েস্ট র্যাটিং থেকে বালশামের দিকে যাওয়া পথটায় শাগ মাঙ্কি নামের এক অদ্ভুত জীব ঘুরে বেড়াত। একটা মোটা চামড়ার কুকুর এবং বড় চোখের বানরের সঙ্কর নাকি ছিল ওটা। কখনও পেছনের পায়ে ভর দিয়ে চলত, কখনও আবার চারপায়ে ছুটে বেড়াত।
নরউইচের কাছের হ্যাম্পনেলের বাসিন্দা মিসেস সোফিয়া উইলসনও কালো কুকুরের অস্তিত্বে প্রবলভাবে বিশ্বাসী। তিনি আমাকে লেখেন, ‘হ্যাম্পনেল থেকে মার্কেট হোল নামে একটি রাস্তা চলে গিয়েছে। একষট্টি বছর আগে যখন হ্যাম্পনেলে প্রথম বাস করতে শুরু করি আমার স্বামী আমাকে বলে এখানকার অনেক বাসিন্দাই এ ধরনের অশুভ একটা কিছু দেখার কথা বলেছেন। আমার প্রিয়তম স্বামী মারা গিয়েছেন। ওই অশুভ কালো কুকুরও আমার কাছে স্রেফ এক কিংবদন্তি হিসাবেই ছিল। তারপরই এক রাতে আমার চব্বিশ বছরের ছেলেটা নরউইচ থেকে যখন এল, দেখলাম ওর চেহারা আতঙ্কে ফ্যাকাসে। সে অসুস্থ কিনা জানতে চাইলে বলল, মার্কেট হল ধরে আসার সময় বিশাল একটা কালো কুকুর তার বাইকের ঠিক মুখোমুখি চলে আসে। সে যখন সংঘর্ষটা এড়াবার কোন উপায় দেখছে না তখন জন্তুটা বেমালুম গায়েব হয়ে যায়। বাইক থেকে নেমে চারপাশে তাকিয়েও সে কিছু দেখতে পায়নি। তখনই ভয় পেয়ে যায়।’
গেলডেস্টোনের ধারের ওয়েভেনে উপত্যকার গ্রামগুলোতেও এ ধরনের অশুভ একটা কিছুর আনাগোনার খবর পাওয়া যায়। সাধারণত বিশাল একটা কুকুরের বেশেই ওটাকে দেখা যায়, তবে কুকুর এত বিশাল হয় না। সাধারণত অশুভ কিছু ঘটতে যাওয়ার আগে ওটা দেখা দেয়।
গ্রামের এক মহিলা জানান, গিলিংহ্যাম থেকে গেলডেস্টোনে যাওয়ার পথে এক রাতে ওটাকে দেখেন। তাঁর বর্ণনায়, ‘আমাদের বিয়ের পর পরই এটা ঘটে। আটটা থেকে নয়টার মাঝামাঝি তখন। গেলডেস্টোনের কাছের একটা লেনে তখন ছিলাম আমরা দু’জন। এসময়ই মিসেস এস.-এর সঙ্গে দেখা হয় আমাদের। তিনজন হাঁটতে শুরু করি। এসময়ই পেছনে একটা শব্দ পাই। অনেকটা একটা কুকুর দৌড়ে আসার মত। ভাবলাম কোন কৃষকের কুকুর। কাজেই মনোযোগ দিলাম না। আমাদের পেছনে লেগে রইল ওটা। পিট! পেট! পিট্! পেট! পিট! পেট!
‘মিসেস এস.-কে জিজ্ঞেস করলাম কুকুরটা কী চায়? ‘চারপাশে তাকিয়ে তিনি বললেন, ‘কোন্ কুকুরের কথা বলছ?’
কেন, তুমি ওটার শব্দ শুনতে পাচ্ছ না?’ অবাক হয়ে জানতে চাইলাম, ‘গত পাঁচ মিনিট কিংবা এর বেশি সময় ধরে জানোয়ারটা আমাদের অনুসরণ করছে। জোস, তুমি শুনতে পাওনি?’
ওহ! পাগল হয়ে গেলে নাকি! কোন শব্দ-টব্দ হচ্ছে না,’ তিরস্কার করল আমার স্বামী, ‘আমার হাতটা ধরে তাড়াতাড়ি পা চালাও।
‘জোস এবং মিসেস এস.-এর মাঝখানে থেকে ভয়ে ভয়ে হাঁটতে লাগলাম।
‘এসময়ই মিসেস এস. বললেন, ‘এখন ওটার শব্দ পেয়েছি। আমাদের সামনে। ওই তো তাকাও!’
‘সত্যি! সামনে একটা জন্তু, বিশাল একটা কালো কুকুরের মতই লাগছে। তবে এটা আসলে কুকুর নয়। অশরীরী কিছু একটা। ভয়ঙ্কর জিনিসটাকে বিভিন্ন জায়গায় দেখা গিয়েছে এর আগে, বেশ অশুভ কিছু ঘটনাও ডেকে এনেছে সে। গির্জার কাছ পর্যন্ত এটা আমাদের আগে আগে চলল। তারপর এক লাফে দেয়াল টপকে সমাধিগুলোর মাঝখানে অদৃশ্য হলো।’
জেলার অনেকেই ওই অশুভ জিনিসটাকে দেখে। তবে ওটার ঘুরে বেড়ানোর প্রিয় জায়গা গেল্ডারস। বিকলস রোডের ধারের একটা জংলা জায়গা এই নামে পরিচিত। এ ব্যাপারে বেশ খোঁজ-খবর নেয়া মি. মোরলে এডামস জানান, কেউ যদি ভয় না পায় তবে কেবল তার পিছু পিছু যাবে জিনিসটা। ওই সময়ে পেছনে তাকানো উচিত না। তাহলে পাগলা কুকুরের মত তেড়ে আসবে। কেউ কেউ বলে রাস্তাঘাট থেকে ছোট ছেলে-মেয়েদের কাপড় কামড়ে টেনে নিয়ে যায় এই মৃত্যুকুকুর।
এসেক্স, ডর্টমুর এসব জায়গায়ও এই অশরীরী কালো কুকুর দেখা যাওয়ার খবর পাওয়া যায়। কালো কুকুরের ডোরচেস্টশায়ারের কিংবদন্তিতে অনুপ্রাণিত হয়েই স্যর আর্থার কোনান ডয়েল লেখেন রহস্যকাহিনী দ্য হাউণ্ড অভ দ্য বাস্কারভিলস।
কালো কুকুরের ব্যাপারে আগ্রহী মানুষের অভাব নেই। ১৯৫৬ সালের ২৯ আগস্ট মিসেস বারবারা কেরবেনেল আমাকে একটা চিঠি লেখেন। এতে ডেভনে এই কালো কুকুরের উপস্থিতি বিষয়ে নানা ধরনের তথ্য দেন।
‘১৯২৫ সালে আবিষ্কার করি নির্দিষ্ট একটা রাস্তা ঘিরে কালো কুকুর দেখা যাওয়ার ঘটনা অনেক বেশি শোনা যায়। কপলস্টোন থেকে টরিংটনের দিকে গেছে রাস্তাটা। মোটামুটি ২১ মাইল এলাকায় এর আনাগোনা বেশি। এক ওয়াগনচালক আমাকে তার অভিজ্ঞতার কথা বলে। পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর বছরের লোকটার সোজাসাপ্টা এবং সত্য কথা বলিয়ে হিসাবে নাম আছে এলাকায়। কপলস্টোনের কারখানাগুলো থেকে টরিংটনে চল্লিশ বছর নিয়মিতই রাতের বেলা জিনিসপত্র আনা- নেয়া করেছে ওয়াগনে করে। প্রথমবার যখন দেখে তখন বেশ নার্ভাস হয়ে পড়েছিল। দ্রুত গিয়ে আশ্রয় নেয় তার বিশাল ওয়াগনের ক্যানভাসের হুডের তলায়। তবে এরপর যখন মাঝে মাঝেই প্রায় ছোটখাট একটা গরুর সমান ওই কালো কুকুরটা দেখা দিতে লাগল রাতে, তখন আর খুব একটা ভয় পায়নি। ঘোড়াগুলোও শুরুতে ওটাকে দেখে ত্রাহি চিৎকার জুড়ে দিত। পরে অভ্যস্ত হয়ে যায়। কুকুরটা ওয়াগনের পাশে পাশে ছুটত। তবে কখনও ওই প্রাণীটাকে সে স্পর্শ করত না, এমনকী ওটার সঙ্গে ভাব আদান-প্রদানেরও চেষ্টা করত না।’
ডেভনের পাহাড়ের ওপর ছোট্ট এক গ্রাম ডাউন সেন্ট মেরি। এখানে একটা প্রাচীন স্যাক্সন গির্জাও আছে। গ্রামবাসীরা জানায় রাতে গির্জার আশপাশে হাজির হয় টরিংটনের কালো কুকুর। বিশেষ করে গ্রামের কামার ওটাকে বেশ কয়েকবারই দেখেছে। গির্জা আর একটা স্কুলঘরের মাঝখান দিয়ে ছুটে যেত অদ্ভুতুড়ে জিনিসটা। এসময় কখনও ওটা মাথা দিয়ে বাড়ি দিত স্কুলদালানকে। এতে ওই দালানের কিনারাটা আংশিক ভেঙেও যায়।
আরেকটা অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে এই গ্রামেরই এক লোক। যুবা বয়সে সে কয়েকজন বন্ধুসহ বড়দিনের উৎসবের রাতের খাওয়া শেষে কপলস্টোনের দিকে ফিরছিল। এসময়ই হঠাৎ কালো কুকুরটার রাস্তা ধরে এগিয়ে আসার শব্দ পায়। তাড়াতাড়ি ওটাকে এড়াতে দৌড়ে একটা মাঠে গিয়ে আশ্রয় নেয় ছেলেরা। দেখে বাছুরের সমান একটা কুকুর, কুচকুচে গায়ের রং, জ্বলজ্বলে চোখ, স্কুলদালানের দিকে ছুটছে। একটু পরেই একটা সংঘর্ষের শব্দ শোনে, অনুমান করে ওটার মাথার আঘাতে স্কুলের দেয়াল থেকে পাথর খসে পড়ছে। এক মুহূর্ত দেরি না করে দৌড়ে বাড়িতে হাজির হয় তারা।
কালো কুকুরের চলাচলের এলাকা হিসাবে যে লাইন বা রাস্তাটা আমি আবিষ্কার করেছি তার সমান্তরালে গিয়েছে উইক হিল নামের এক গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমের এক খাড়া পাহাড়ি রাস্তা। ওখানে অ্যালেন’স উইক নামে একটা খামারও আছে। এখানে কোন ঘটনা জানতে পারি ভেবে খোঁজ-খবর নেয়ার চিন্তা করি। তারপরই মনে পড়ে আমাদের গ্রামের দোকানটা যে মহিলা চালায় সে একসময় ওখানে থাকত। তার বাবা এখনও ওই এলাকাতেই থাকেন। দোকানে এসে জানতে চাইলাম, ‘টরিংটনের কালো কুকুরের কথা কি শুনেছ?’
আমি যখন কথা বলছিলাম তখনই গ্রামের দু’জন মহিলা ভেতরে ঢুকল কিছু কিনতে। দোকানি মিসেস জুয়েল খুব আলাপী এবং ভাল মানুষ। কিন্তু হঠাৎই সে বলে উঠল, ‘না, কখনওই না।’ তারপর আমাকে বিদায় জানিয়ে ওই দুই মহিলার সঙ্গে আলাপ শুরু করল।
তার এই ব্যবহারে হতবিহ্বল হয়ে চলে গেলাম। আধ ঘণ্টাটাক পরে আবার যখন দোকানের সামনে দিয়ে যাচ্ছি মিসেস জুয়েল দরজার সামনে এল। আমার বাহু ধরে বলল, ‘মনে কষ্ট নিয়ো না। এসো, তোমাকে অনেক কথাই বলার আছে আমার।’ তারপর টেনে তার পার্লারে নিয়ে গেল আমাকে।
‘টরিংটনের কালো কুকুরের ব্যাপারে তুমি কী জানতে চাও?’
জবাবে জানালাম এই কুকুরটার বিশেষ করে উইক হিলের আশপাশে এর বিচরণের ঘটনাগুলো নিয়ে জানতে আগ্রহী আমি।
কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল মহিলা। হয়তো সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। তারপর ঝেড়ে কাশল, ‘ওটা সবসময়ই ওখানে আছে। সবাই প্রাণীটার কথা জানে। তবে ওটার কথা বললে মন্দভাগ্য তাড়া করে। আমি জানি না তোমাকে কুকুরটার কথা বলে নিজের বিপদ টেনে আনছি কিনা।
তারপর ফিসফিস করে বলতে শুরু করল। সে চাইছিল না এখানকার কেউ তার এই কথা শুনুক। উইক হিলেই বেশি আসে ওটা। ওখানেই প্রথম দেখে। তখন তার বয়স এই দশ। ১৮৭০ সাল কি এর দু’এক বছর আগে বা পরের ঘটনা। রাত এগারোটা। বাবার সঙ্গে একটা উৎসবের খাওয়া শেষে বাড়ি ফিরছিল। উইক’ হিলের অ্যালেন’স উইক খামারের কাছেই তাদের বাড়ি। চন্দ্রালোকিত এক রাত ছিল সেটা। হঠাৎ তাদের পেছনে একটা কিছুর শব্দ শুনে সচকিত হয়ে ওঠে দু’জনে। পিছু পিছু আসছে একটা বিশাল কালো কুকুরের মত জন্তু। বাবার হাত চেপে ধরে চিৎকার করে ওঠে সে। বাবা বলেন তখন, ‘আমার হাত ধরো, কথা বলবে না একটুও। আস্তে হাঁটো, কাঁদবে না।’
মোটামুটি সিকি মাইল জন্তুটা তাদের পেছন পেছন আসে। ওটার জিভটা বেরিয়ে ছিল মুখ থেকে। টকটকে লাল। একপর্যায়ে সে এবং তার বাবা যখন রাস্তা ছেড়ে কটেজের দিকে চলে যায় কুকুরটা তাদের গেটের পাশ দিয়ে ছুটে অদৃশ্য হয়। তার বাবা তখন বলেন, এই অশরীরী কুকুরটা বহু বছর ধরে এভাবেই মাঝে মাঝে চেহারা দেখিয়ে আসছে। কারও ক্ষতি করে না। মিসেস জুয়েল জানায়, পর পর কয়েক রাত ওটার কথা ভেবে ঘুম হয়নি তার।
চোদ্দ বছর বয়সে আবার কুকুরটা দেখে সে। সমবয়সী দুটি মেয়ের সঙ্গে একটা ফার্ম থেকে ফিরছিল। উইক হিলের দিকে যাওয়া একটা মেঠো পথ পেরোচ্ছিল মেয়েরা। তিনজনই দেখে মাটিতে নাক প্রায় ঠেকিয়ে দৌড়চ্ছে বিশাল ওই জানোয়ারটা, আর প্রচণ্ড শব্দে গর্জাচ্ছে। মনে হচ্ছিল কুকুরদের গোটা একটা দল চিৎকার করছে খেপে গিয়ে। আরেকবার বাড়িতে পৌছার ঠিক আগে তাকে অতিক্রম করে যায় কুকুরটা। ওটার পথ থেকে লাফিয়ে সরে যায় সে, আর কুকুরটা পরমুহূর্তে হঠাৎই অদৃশ্য হয়।
বহু বছর পর, তার বিয়ে হয়ে গিয়েছে ততদিনে, টরিংটন মার্কেট থেকে একটা টাট্টুতে চেপে ফিরছিল বাবার সঙ্গে। টরিংটন এবং অ্যালেন’স উইকের মাঝখানে হঠাৎ একটা ডোবামত জায়গা থেকে লাফিয়ে তাদের সামনে চলে আসে ওই অশুভ কালো জন্তুটা। টাট্টুটা এতটাই ভয় পেয়ে যায় যে, পাগলের মত ছুটতে শুরু করে তাদের নিয়ে। সে আমাকে এটাও জানায় কিছুদিন আগেও (১৯২৫-২৬) ওই এলাকায় একে দেখা গিয়েছে। যদিও বিষয়টা নিয়ে কেউ মুখ খোলেনি।
১৯৩২ সালের ঘটনা। বিডফোর্ডের দুই মাইল দূরে এক যাজকের বাড়িতে বাস করছিলাম আমরা। ওই সময় আমার বোন এবং তার স্বামীও ছিল আমাদের সঙ্গে। বোন জামাইয়ের তখন ছুটি চলছিল। জানুয়ারির এক রাতে উইংলেইফে এক আত্মীয়ের বাড়িতে ডিনারের দাওয়াতে গিয়েছিল স্বামী-স্ত্রী। ফেরে মধ্যরাতের একটু পরে। টরিংটন থেকে বিডফোর্ডের রাস্তাটা পড়ে তাদের এই যাত্রায়। ঘুমিয়ে পড়ায় রাতে তাদের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। পরদিন সকালে নাস্তার টেবিলে আমার বোন জানতে চায় বিডফোর্ড এবং উইংলেইফের মাঝখানের পথে কালো কুকুরের দেখা দেয়ার ব্যাপারে কিছু জানি কিনা। জবাবে জানাই ওই রাস্তায় এ ধরনের কিছুর কথা শুনিনি। তখন আমার বোন আমাকে তাদের গত রাতের অভিজ্ঞতাটা বলে।
টরিজের পাশের ফ্রিথেলস্টকের নিচের রাস্তা ধরে গাড়ি চালিয়ে আসছিল তারা। হঠাৎ গাড়ির হেডলাইটের আলোয় যেটাকে দেখা গেল সেটা দেখতে কুকুরের মত হলেও এত বিশাল কুকুর কোন মানুষ কখনও দেখেছে কিনা বলতে পারবে না। ওটা তাদের এতটাই কাছে ছিল যে সংঘর্ষ এড়াবার জন্য কড়া ব্রেক কষতে হলো তার স্বামীকে। তারপরও তাদের ধারণা ছিল কুকুরটা আঘাত পেয়েছে। কিন্তু গাড়ি থামার পর কোথাও দেখা গেল না ওটাকে।
আমার ম্যাপটা এনে সামনে মেলে দিতেই ওরা আমাকে দেখাল কোথায় ঘটনাটা ঘটে। ওখান থেকে সরতে হলে জন্তুটাকে হয় এক পাশের খাড়া পাথুরে পাহাড় বাইতে হত, নইলে উঁচু দেয়াল লাফিয়ে টপকে নদীতে পড়তে হত। কিন্তু কোনটাই সম্ভব নয়।
আমার বোন সকালরেলায়ও ওই ঘটনাটার কথা মনে করে কাঁপছিল। কোন কুকুর হতেই পারে না ওটা, এটা তার বিশ্বাস। এদিকে আমার বোনের স্বামী সবসময়ই একজন অতি যুক্তিবাদী মানুষ। তার মতে সব অদ্ভুত ঘটনারই কোন না কোন জাগতিক ব্যাখ্যা থাকতে বাধ্য। কিন্তু সে আমাকে বলল বিশাল ওই জিনিসটার হঠাৎ শূন্য থেকে হাজির হওয়া কিংবা আবার ওটার মিলিয়ে যাওয়ার কোন ব্যাখ্যা অন্তত তার কাছে নেই।
আশি বছর বয়সী মি. ফ্রিম্যান, একসময় যিনি যাজক ছিলেন, আমাকে ১৯২৩ সালে বলেন, ট্রভেরটনে এখনও কালো কুকুরটাকে দেখা যাওয়ার ঘটনা ঘটে।
লাইম রেজিসের সীমানার ঠিক বাইরে, একটা লেনের কিনারে এক সরাইখানা আছে, যেটার নাম ব্ল্যাক ডগ বা কালো কুকুর সরাইখানা। বলা হয় রাতের বেলা একটা বিশাল কুকুর ছুটে এসে ওই সরাইখানার এক কিনারার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। এতে হঠাৎ হঠাৎ ওই অংশের দেয়াল ধসে যেত।
থেলব্রিজের কাছে একটা জায়গা আছে যার নাম ব্ল্যাক ডগ। উনিশশো সালের দিকে ওখানে এমনকী স্থায়ী. একটা ছোট বসতিও ছিল না। কেবল ছিল একই নামের একটা সরাইখানা এবং এক কামারশালা।
ট্রভেরটনের চৌহদ্দিতেও কালো কুকুরের কিংবদন্তি ডালপালা মেলেছে। ওখানে বাস করা ব্ল্যাকমোর নামের উচ্চশিক্ষিত এক ভদ্রলোক বলেছিলেন তিনি এবং তাঁর বাবা দু’জনেই ভয়াল ওই কালো কুকুরকে দেখেছেন। শুধু তা-ই না, এক প্রজন্মের পর আরেক প্রজন্ম ধরে লোকেরা একে দেখে আসছে। কীভাবে এটা সম্ভব তাঁর জানা নেই।
ডেভনে কালো কুকুরটার উপস্থিতির ব্যাপারে মিসেস কেরবেনেলের এই গবেষণার পর আশা করি পাঠকদের পক্ষে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনো সম্ভব হবে।
এখানে বর্ণনা করা বেশিরভাগ ঘটনাই আশি-নব্বই বছর কিংবা আরও বেশি আগের। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের বিভিন্ন জায়গায় এখনও কালো কুকুর দেখা যাওয়ার ঘটনা শোনা যায়। ভবিষ্যতে সত্য হরর কাহিনী সিরিজের অন্য কোন পর্বে কালো কুকুরের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো নিয়ে লেখার ইচ্ছা রইল।
নার্স ব্ল্যাক
১৮৫০-এর দশকে চার্লস কিন এবং তাঁর স্ত্রী অ্যালেন ইংল্যাণ্ডের মঞ্চে ছিলেন অতি পরিচিত মুখ। অভিনেতা- অভিনেত্রী ও ম্যানেজার দুই ভূমিকাতেই তাঁরা ছিলেন সফল। নানা ধরনের বিচিত্র বিষয়ের প্রতিও ঝোঁক ছিল এই দম্পতির। কাজেই তাঁদের এক নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে যখন ভৌতিক ঘটনা ঘটল বিস্তারিত বর্ণনাসহ তা লিপিবদ্ধ করেন কিন। আর তাঁর মাধ্যমে এর কাহিনীটা আসায় এ নিয়ে সন্দেহের অবকাশ কম।
মিসেস কিনের বোন অ্যান ট্রির সঙ্গে বিয়ে হয় জন ক্যাম্বল চ্যাপম্যানের। একসময়ের এই থিয়েটার ম্যানেজার তখন বিখ্যাত এক প্রকাশক। তাঁদের পরিবারটি ছিল বিশাল। মোটমাট এগারোটি সন্তান ছিল ওই দম্পতির। ছোট বাচ্চাগুলোর জন্য লণ্ডনের আবহাওয়া একটু অস্বাস্থ্যকর মনে হওয়ায় তাঁরা একটু মফস্বল এলাকায় সরে পড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।
হার্টফোর্ডশায়ারের চেসহান্টে একটা বাড়ি পছন্দ হয় তাঁদের। ওটার মালিক স্যর হেনরি মিউক্স। এই বিশাল পরিবারের সদস্যদের দেখভালের জন্য ছিল জনা আটেক চাকর-কর্মচারী। তবে বাড়িটা এত বড় যে সবারই জায়গা হয়ে গেল হেসে-খেলে। বড় মাঠ, লন এমনকী কিছু উঁচু গাছও আছে। চাই কী এগুলো বেয়ে উঠে দুরন্তপনার পরীক্ষাও দিতে পারে তারা। মিসেস চ্যাপম্যান গোটা বাড়িটা ঘুরে-ফিরে দেখে স্বাভাবিকভাবেই খুব খুশি।
প্রায় দুইশো বছরের পুরানো বাড়িটা সতেরো শতকের শেষভাগের কোন একসময় বানানো হয়েছে। প্রাচীন ওক গাছের খাম্বা খাড়া করে রেখেছে দালানটাকে। ফায়ারপ্লেসগুলো বড় আর নকশা করা। মাঝখানে একটা চওড়া সিঁড়ির পাশাপাশি দুই পাশে ভৃত্যদের ব্যবহারের জন্য সরু দুটো সর্পিলাকার সিঁড়িও আছে। ছোট শিশুদের খেলার জন্য আছে একটি আলাদা ঘর বা নার্সারি। এর পাশাপাশি চিলেকোঠায় কয়েকটা ঘর আবিষ্কার করে বাচ্চারা এবং এতে তাদের দেখভালের দায়িত্বে থাকা ভৃত্যরা দারুণ খুশি হয়ে উঠল।
সাপ্তাহিক ছুটির দিনে মুক্ত বাতাসের লোভে জন চ্যাপম্যানের অনেক বন্ধু-বান্ধবই এখানে হাজির হয়ে যান। এই দম্পতি সবসময়ই দিল-দরিয়া ও অতিথিবৎসল। লণ্ডনের বন্ধুদের তা অজানাও নয়। এদিকে জন চ্যাপম্যানও সপ্তাহে দু-একটা দিন ব্যবসার প্রয়োজনে লণ্ডনে কাটিয়ে দেন। কখনও স্ত্রীকেও সঙ্গে নিয়ে যান। এখানকার বাড়িতে দু- একটা কামরা সবসময়ই অতিথিদের জন্য তৈরি রাখা হয়। হঠাৎ জানান না দিয়ে হাজির হয়ে গেলেও বিন্দুমাত্র বিরক্ত হন না অ্যান চ্যাপম্যান। এক কথায় চমৎকার, আধুনিকা এক নারী তিনি। জন মাঝে মাঝেই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানান এমন একজন আদর্শ স্ত্রী পাবার জন্য।
অ্যান কোন হাউসকিপার রাখেননি। নিজেই বাড়ির বিষয় তদারক করেন। কোন অতিথি আসার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সব ধরনের প্রস্তুতি নেয়ার ব্যবস্থা করেন। শুধু তাই না, অতিথিরা যে কামরাগুলোতে থাকবেন নিজে একবার সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে আসেন। এদের মধ্যে সেরাটা বরাদ্দ থাকে গুরুত্বপূর্ণ বা তাঁদের খুব কাছের মানুষদের জন্য। ওই কামরাটা পরিচিত ওক বেডরুম নামে। ভারী ওকের প্যানেল, বিশাল খাট এবং পর্দায় ওক পাতার ছবির কারণেই এমন নামকরণ। কামরাটা একটু অন্ধকার হলেও সবার বেশ পছন্দ হয় এর আভিজাত্যের জন্য। অ্যান এই কামরাটা সবসময় যেন রেডি থাকে এ বিষয়ে চোখ-কান একটু বেশিই খোলা রাখেন।
শরতের এক সন্ধ্যা। ধীরে ধীরে অন্ধকাররা আলোদের হটিয়ে জায়গা দখল করে নিচ্ছে। কয়েকটা বালিশ নিয়ে ওক বেডরুমের সামনে হাজির হলেন অ্যান। এক লেখক বন্ধুকে বাড়িতে নিয়ে এসেছেন জন। ফ্লিট স্ট্রিটের অফিসের গোলমালের চেয়ে তাঁর লেখার বিষয়ে বাড়ির শান্ত পরিবেশে আলাপ করাটাই ভাল মনে হয়েছে। বালিশগুলোর তদারকিতে যে মেয়েটা সে একেবারেই নতুন এসেছে। তাই নিজেই বিষয়টা দেখভাল করছেন অ্যান।
ওক বেডরুমের তালাটা পুরানো। ওটা খুলতে একটু ঝক্কি পোহাতে হয়। হাতে বালিশ থাকায় আরও বেশি বেগ পেতে হলো অ্যানকে। যখন কামরায় ঢুকলেন বোঝাটা নামিয়ে রেখে একটা মোমবাতির খোঁজ করলেন আলো জ্বালতে। এই কামরাটায় বিছানাটা ঠিকঠাক করার জন্য এটা দরকার।
মোমবাতির খোঁজে যখন হাত বাড়ালেন তখনই একটা জিনিস আবিষ্কার করে থমকে গেলেন। কামরাটায় তিনি একা নন। দূরের জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক নারী। এক পলকেই অ্যান বুঝে গেলেন সে হালকা-পাতলা দেহের এক তরুণী। লম্বা চুল নেমে গেছে অনেকটা পর্যন্ত। পশমী পেটিকোটের ওপর সাদা একটা শাল চাপিয়েছে। জানালা গলে আসা আবছা আলোতেঁ সিল্কের কাপড়টা ঝিকমিক করে উঠতে দেখলেন অ্যান। ব্যগ্রভাবে সামনের দিকে ঝুঁকে আছে মেয়েটা, জানালা দিয়ে যেন নিচের বাগানে কিছু একটা দেখছে।
খুব একটা চিন্তা না করেও অ্যানের মনে পড়ে গেল, ভৃত্যরা সবাই চা খাচ্ছে, আর ছেলে-মেয়েরা নার্সারিতে। এটা তাদের কেউ নয়। একটা সম্ভাবনাই বাকি আছে, তা হলো অচেনা কেউ কোনভাবে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। কিন্তু অ্যান বুঝতে পারলেন সিঁড়ি পেরিয়ে এখানে আসা তার পক্ষে অসম্ভব, কেউ না কেউ দেখতই। হঠাৎই অ্যানের মনে হলো স্বাভাবিক কোন কিছু দেখছেন না তিনি। ভয়ে কেঁপে উঠল শরীরটা। কী মনে করে চোখের সামনে একটা হাত নিয়ে এলেন। যখন ওটা সরালেন মেয়েটা অদৃশ্য হয়েছে।
রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তাঁর আতঙ্কে। তবে ভয়ে নিজের কাজ থেকে বিরত থাকবেন এমন মহিলা তিনি নন। কাঁপতে থাকা হাতে বিছানাটা গোছগাছ করলেন।
ঘটনাটা কাউকে বললেন না, এমনকী স্বামীকেও। পরদিন সকালে যখন অতিথি নাস্তা করতে খাবার রুমে এলেন, আশঙ্কা নিয়ে তাঁর দিকে তাকালেন অ্যান। তিনি কী বলেন এটা ভেবে। নাকি এখনই একটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে তাঁকে লণ্ডন পৌঁছে দিতে বলেন আবার। কিন্তু তাঁকে বেশ হাসি- খুশিই দেখাল। বরং গৃহকর্ত্রীকে আরামদায়ক শয্যা এবং কামরার জন্য ধন্যবাদ দিলেন। অ্যান মনে মনেই বললেন, তবে কি ভুল দেখেছেন? আলোর খেলা ছিল ওটা? কই, অতিথির তো কোন সমস্যাই হয়নি রাতে!
কয়েকদিনের মধ্যেই আরও বড় চমকটা হাজির হলো অ্যানের জন্য। ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে নার্সারিতে সময় কাটানো মেয়েটা, কিটি ব্রকেট যার নাম, হাজির হলো কাঁদতে কাঁদতে। আতঙ্কে কাঁপছে সে। এতটাই ভয় পেয়েছে যে প্রথমে কী বলছে বোঝাই গেল না। তবে একটু ধৈর্য ধরে প্রশ্ন করে অ্যান বুঝতে পারলেন সমস্যাটা কোথায়। নার্সারির ময়লাগুলো বাড়ির পেছনের ভাগাড়ে ফেলতে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিল সে। এসময়ই বাইরের উঠনের দিকের ছোট্ট জানালাটায় একটা মুখ দেখতে পায়। চেহারাটা কেন তাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে এটা বোঝানো বেশ কষ্টকর হলো কিটির জন্য। তবে তার এলোমেলো কথা থেকে অ্যান বুঝতে পারলেন বুড়ি এক মহিলার মুখ ওটা। ভয়ানক কুৎসিত। চুল ঢাকা ছিল পুরানো আমলের ক্যাপ দিয়ে। সবচেয়ে বড় কথা তার দৃষ্টিটা ছিল অশুভ।
মেয়েটার ভয় বাড়িয়ে দেয়ার কোন ইচ্ছাই অ্যানের নেই। তাই বললেন ওটা নিশ্চয়ই এক বুড়ি জিপসি। কাউন্টির এই অংশে এরা অনেকই আছে। কিটি তখন জিজ্ঞেস করল, তাহলে ওই মহিলা উঠনে ঢুকল কেমন করে? একমাত্র রান্নাঘর ছাড়া আর কোন পথ নেই ওখানে ঢোকার। রাঁধুনি নিশ্চয়ই একজন জিপসি বুড়িকে তার পাশ দিয়ে চলে যেতে দেবে না? অ্যানকে স্বীকার করতে হলো বিষয়টা রহস্যময়। মেয়েটার ভয় দূর করতে দু’জন মিলে ছোট্ট জানালাটা দিয়ে তাকালেন উঠনের দিকে। জায়গাটা খালি। রাঁধুনির সঙ্গে কথা বলতে জানাল তার কাছে জিপসি মহিলা তো নয়ই, কেউই আসেনি আজ সকালে। অ্যান মেয়েটাকে বললেন, মনে হয় আলোর কারসাজিতে ধোঁকা খেয়েছে সে।
দুই রাত পর নতুন একটা ঘটনা হাজির হলো অ্যানের সামনে। বাড়ির একজন মেইড রাতে চড়া একটা শব্দ শুনতে পায়। যেন উঠনে লোহার ডাণ্ডা দিয়ে কিছু একটা পিটাচ্ছে কেউ। তার খাস কামরার পাশেই জায়গাটি। এদিকে আগের ওই তরুণী মেয়েটা, মানে কিটি নিশ্চিত করল গত রাতে সে-ও ওই একই ধরনের শব্দ শুনেছে। রান্নাঘরে দুধ গরম করতে গিয়েছিল তখন।
পরের কাহিনীটার উদ্ভব হলো নার্সারি থেকে। ছোট্ট মারিয়া, বেশ সাহসী সে, অতিরিক্ত কল্পনাপ্রবণও নয়, বলল ঘুম থেকে জেগে দেখে নার্সারির দরজার কিনারা দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে বিশ্রী, কদাকার চেহারার এক বুড়ি। মা তাকে বুঝিয়ে বললেন, এটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু অ্যান ঠিকই বুঝতে পারলেন মেয়ে সত্যিই অশুভ বুড়িকে দেখেছে!
পুরো হপ্তাটাই জন চ্যাপম্যান লণ্ডনে কাটিয়েছেন। শুক্রবার রাতে বাড়িতে ফিরবেন ভেবে বেশ শান্তি লাগছে অ্যানের। ছেলে-মেয়ে ও কর্মচারীদের সামনে হাসি-খুশি থাকার অভিনয় চালিয়ে যেতে যেতে রীতিমত অধৈর্য হয়ে পড়ছিলেন। এই গ্রাম এলাকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন মেয়েগুলো একবার গোটা বিষয়টার সঙ্গে ভূত-প্রেতের সম্পর্ক আছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হলেই হয়েছে! অ্যান ভয় পাচ্ছেন এই মেয়েদের কে আবার তাঁর সামনে হাজির হয়ে চাকরি ছাড়ার নোটিশ দেয়! তাছাড়া তাঁর নিজের জন্যও এই ঘটনাগুলোর বাস্তবসম্মত একটা ব্যাখ্যা জানা প্রয়োজন। একপর্যায়ে রহস্যটা সমাধান করার শেষ চেষ্টা হিসাবে বাড়ির সব ভৃত্যকে ডেকে বললেন তাঁদের বাড়ির আশপাশে জিপসিদের আসার খবর মিলেছে। চুরি-ডাকাতি করার জন্য কেউ আবার ভেতরে লুকিয়ে আছে কিনা দেখার জন্য তল্লাশি চালাতে হবে। মেয়েরা যথেষ্ট আগ্রহ নিয়েই কাজ করল। প্রতিটি আলমারি, প্যানেল, পাতালঘর, চিলেকোঠা থেকে শুরু করে বাড়ির এমনকী বাইরের ঘরগুলোর আনাচে-কানাচে খোঁজা হলো। কিন্তু কোন জিপসির নাম-গন্ধও পাওয়া গেল না। অবশ্য তিনি যে তাতে খুব একটা বিস্মিত হলেন তা না।
জন চ্যাপম্যান আসার সময় সমাগত হতেই অধীর আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন অ্যান। কিন্তু যখন এলেন, দেখা গেল একা আসেননি। সঙ্গে প্রকাশনা সংস্থার সদস্য মি. হলকে নিয়ে এসেছেন। অ্যান তাঁকে হাসিমুখে স্বাগত জানালেন। যখন দেখলেন ভদ্রলোক স্বামীর সঙ্গে গল্প করছেন, সিঁড়ি ধরে ওক রুমের দিকে রওয়ানা হলেন ওটাকে রাতে অতিথি থাকার জন্য প্রস্তুত করতে।
স্বামী ঘরে ফেরাতে বেশ নির্ভার লাগছে তাঁর। আপাতত এমনকী ভুতুড়ে কাণ্ড-কীর্তির কথাও বিস্মৃত হয়েছেন। এসময়ই হঠাৎ চওড়া সিঁড়িতে তাঁর পেছনে পদশব্দ শুনলেন। ঘাড় ফেরালেন কে দেখবার জন্য।
কেউ নেই। সিঁড়িটা একেবারে খালি, নিচে ছায়াময় হলওয়েতেও কাউকে দেখা যাচ্ছে না।
আতঙ্কিত হয়ে দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে আবার নিচে নেমে, ছেলে-মেয়েদের নার্সারিতে হাজির হলেন। তাদের হৈ চৈ আর কোলাহলে একটু একটু করে স্বাভাবিক হলেন। রাতের খাবারের আগ পর্যন্ত ওখানেই কাটালেন। ডিনারটা সবাই চমৎকারভাবেই সারলেন। পুরুষরা স্টাডিতে সিগার টানতে টানতে আলাপ করতে লাগলেন, অ্যান বসলেন সুঁই-সুতো নিয়ে। কয়েক মুহূর্ত পর দরজায় একটা নক হলো। বৈঠকখানার দায়িত্বে আছে মধ্যবয়স্ক মহিলাটি। মিসেস টেওয়িন নামেই সে পরিচিত। এমনিতে শান্ত স্বভাবের ও ধীর-স্থির হলেও কামরায় ঢুকল যখন তাকে খুব বিপর্যস্ত দেখাল। চেহারাটা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে, কাঁপছে থরথর করে। অদৃশ্য কারও পায়ের আওয়াজ শুনেছে সে, জানতে পারলেন অ্যান। সিঁড়ি বেয়ে ওক রুমে যাওয়া পর্যন্ত পায়ের আওয়াজটা তাকে অনুসরণ করেছে, সে যখন ঢুকেছে তখনও শব্দটা ভেতরে ঢুকেছে। যখন ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়িয়েছে মিসেস টেওয়িন, তখন শব্দটাও থেমে যায়। কয়েক রাত আগে এই মহিলা দরজায় নক করার আওয়াজ শুনেছে। এবারের ঘটনায় এতটাই ভয় পেয়ে গেছে যে চাকরি ছাড়তে চাইছে।
অ্যান তাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে শান্ত করে বললেন, সকালে বিষয়টা নিয়ে ভাবা যাবে। যা হোক, একটু পানি মিশানো ব্র্যাণ্ডি খেয়ে ঘুমাতে গেল মহিলা।
ওই রাতে স্বামীকে সব কিছু খুলে বললেন অ্যান। অনেক স্বামীই হয়তো বৃত্তান্ত শুনে অট্টহাসিতে ফেটে পড়তেন। স্ত্রীকে একটু কম কল্পনাপ্রবণ হওয়ার পরামর্শ দিতেন। কিন্তু থিয়েটারের সঙ্গে দীর্ঘদিন জড়িত থাকায় এ ধরনের অতিপ্রাকৃত বিষয়ের প্রতি বেশ আগ্রহ জন্মেছে জনের। শুধু তাই না এমনটা যে ঘটতে পারে এটা মনেও করেন। অ্যানকে ‘জড়িয়ে ধরে বললেন, আগামী হপ্তাটা এখানে থেকেই কাজ করবেন তিনি। আর নিজেই রহস্যটা সমাধানের চেষ্টা করবেন।
তাঁকে হতাশ হতে হলো না। পরের কয়েকদিন এই অদৃশ্য পদশব্দ শোনা গেল। কয়েকটা ভৃত্য এবং বড় দুই মেয়ে শব্দটা শুনল। শুধু যে ওক বেডরুম এবং সিঁড়িতেই আওয়াজ শুনেছে তা নয়, বাড়ির আরও নানা প্রান্তেই পায়ের আওয়াজ শোনা গিয়েছে। এক রাতের ঘটনা। বিছানায় শুয়ে আছেন অ্যান। হঠাৎ দরজার দিকে পদশব্দ শুনতে পেলেন। এক ছুটে গিয়ে দরজা খুললেন। কিন্তু ল্যাণ্ডিং একেবারে খাঁ খাঁ করছে। পরের রাতে জন দেখলেন ‘বালিশের নিচে কিছু একটা লুকাচ্ছেন অ্যান। ঘটনাটা কী জানতে চাইলে কিছু বললেন না তাঁর স্ত্রী। নিজে খোঁজ করতেই আবিষ্কার করলেন একটা রিভলভার। এবার মুখ খুললেন অ্যান। অশরীরীটার মোকাবেলা করতে ওটা রেখেছেন। জন বললেন এতে কোন লাভ তো হবেই না, উল্টো বাড়ির লোকজন আহত হতে পারে। বুঝতে পেরে বালিশের নিচ থেকে রিভলভার সরালেন অ্যান, তবে নাগালের মধ্যেই রাখলেন অস্ত্রটা।
এমনকী এখন ভৃত্যদের সামনেও আর অস্বাভাবিক কিছু ঘটছে না এমন ভান করেন না অ্যান। ভয়ানক একটা কিছু বাড়ির মধ্যে ঘোরাফেরা করছে বুঝতে পেরে চাকর-বাকররা বাড়ির ভেতরেই দল বেঁধে চলাফেরা করে। বিশেষ করে বড় দুই মেয়ে পেটি এবং মারিয়ার মধ্যেও ভয়টা ছড়িয়ে পড়েছে। রাতে নার্সারিতে আবারও ভয়ানক মুখটা দেখা যাবার পর ছোট ছেলে-মেয়েগুলোও কেমন একটা অস্বস্তিতে পড়ে গেছে। এক রাতের ঘটনা। ভৃত্যরা ডিনারে বসেছে। হঠাৎ কামরার দরজাটার খিলে টান পড়ল। তারপরই আস্তে আস্তে খুলে গেল দরজাটা। কাউকে দেখা গেল না। আবার বন্ধ হয়ে গেল। সবাই ভয়ে পেয়ে গেল। একটা মেয়ে জ্ঞান হারাল। কিটি চিৎকার শুরু করে দিল উন্মত্তের মত।
জন চ্যাপম্যান সব কিছু শুনে পরের দিন চাকরদের ডিনারের সময় ওই কামরাটায় রইলেন, যদি আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। সত্যিই তা-ই ঘটল। সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে গিয়েও এই রহস্যময় দরজা খোলা ও বন্ধ হওয়ার পেছনে কার ভূমিকা তা উদ্ঘাটন করতে পারলেন না। তবে কাজটা যে রক্ত-মাংসের কারও নয় তা বুঝতে অসুবিধা হলো না।
পরদিন বিকালে জরুরি কাজে লণ্ডনে যেতেই হলো জনকে। স্ত্রীকে বললেন রাতে কামরায় সঙ্গে একজন ভৃত্যকে রাখতে। মিসেস টেওয়িনকে বেছে নিলেন অ্যান। চ্যাপম্যানদের বেডরুমের কোনার ছোট্ট বিছানাটায় ঘুমাবে সে।
রাত আনুমানিক একটার দিকে অপর খাটে বিড়বিড় শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল অ্যানের। ‘আমাকে জাগাও! আমাকে জাগাও!’ বলছে মিসেস টেওয়িন। চোখদুটো বন্ধ, তবে মুখে যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্ট। নিজের বিছানা থেকে লাফ দিয়ে নেমে মহিলাকে ধাক্কা দিয়ে জাগালেন। মালকিনকে ভয়ানক এক দুঃস্বপ্নের কবল থেকে তাকে বাঁচানোর জন্য ধন্যবাদ দিল মিসেস টেওয়িন। জেগে ওঠার প্রাণপণ চেষ্টা করেও সফল হচ্ছিল না সে।
বলল স্বপ্নে সে চলে গিয়েছিল ওক রুমের বিছানায়। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল এক তরুণী। ফ্যাকাসে মুখ। লম্বা, ঘন কালো চুল তার। গায়ে ছিল পুরানো দিনের সাদা ঢিলে গাউন বা রোব। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে কামরার অপর একটা মহিলার দিকে তাকিয়ে ছিল। বিছানার পাশে ফায়ারপ্লেসের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল সে। এই মহিলাটাই ভয় পাইয়ে দেয় মিসেস টেওয়িনকে। অদ্ভুত রকম অপরিচ্ছন্ন মহিলাটি, তবে চেহারাটা এতটাই অশুভ যে ভাবলে এখনও গা শিরশির করে উঠছে। তার পরনেও ছিল পুরানো ফ্যাশনের পোশাক। দুর্গন্ধে ভরা ধূসর চুলের ওপর চাপিয়েছিল একটা টুপি।
‘বাচ্চাটাকে তুমি কী করেছ, এমিলি? কী করেছ বলো!’ ব্যঙ্গ করে সে জিজ্ঞেস করল তরুণীকে।
‘ওহ! আমি ওকে মারিনি। ওকে রক্ষা করেছি। বড় হয়ে নম্বর রেজিমেন্টে যোগ দিয়ে ভারত গিয়েছে।’
তারপর তরুণী বিছানার কাছে এসে ঘুমন্ত মহিলাকে সরাসরি বলল, ‘আগে কখনও কাউকে বলিনি। তবে তোমাকে বলছি এখন। আমার নাম মিস ব্ল্যাক। আর ওই বুড়ির নাম নার্স ব্ল্যাক। এটা তার নাম নয়, তবে আমাদের পরিবারের সঙ্গে অনেক দিন ধরে থাকায় এই নামেই তাকে ডাকি আমরা।’
এ পরিস্থিতিতে বিছানার সামনে হাজির হয়ে বুড়ি তার কথায় বাধা দেয় এবং ঘুমন্ত মিসেস টেওয়িনের কাঁধে হাত রাখে। কিছু একটা বলে। যেটা মনে করতে পারছে না এখন। তবে যে জায়গাটিতে অশুভ মহিলা হাত বুলিয়েছে সেখানে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হচ্ছে। সে বুঝতে পারছিল তার জেগে ওঠার দরকার। তাই মালকিনকে ডাকছিল।
পরের দিন সকালেই বেরিয়ে পড়েন অ্যান। এই বাড়ি আর এর পুরানো বাসিন্দাদের ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতে। কেউ তেমন কিছু বলতে না পারলেও এই এলাকার পুরানো, এক বাসিন্দা কিছু তথ্য দিলেন। সত্তর-আশি বছর আগে, এই ১৭৭৫-এর দিকে, মিসেস রেভেনহল নামের এক ভদ্রমহিলা ওই বাড়িতে থাকতেন। তাঁর এক ভাতিজি, যার নাম মিস ব্ল্যাক, মহিলার সঙ্গে থাকত। এর বাইরে আর কিছু জানেন না ওই ভদ্রলোক।
তবে মিসেস অ্যানের সাহসের প্রশংসা করতেই হয়। কারণ এরপর এক রাত একা ওক রুমে ঘুমালেন তিনি। আবারও সেই সাদা তরুণীকে দেখলেন, এবার কামরার এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। কাঁদছে, হাত ঝাঁকাচ্ছে। নিচে মেঝের দিকে তাকিয়ে আছে বেদনার্ত চোখে। পরের দিন এক মিস্ত্রীকে ডাকা হলো মেঝের ওই অংশের কাঠের পাটাতন তুলে ফেলতে। তবে একসময় ওখানে যা-ই থাকুক না কেন নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে অস্বাভাবিক ঘটনা কমতে লাগল বাড়িটাতে। একপর্যায়ে থেমে গেল একেবারে। বেশ নিশ্চিন্ত হলো পরিবারটি। কিন্তু তখনও একটা ঘটনা ঘটার বাকি। রহস্যময় ঘটনা শুরুর কয়েক বছর পর ব্যবসার প্রয়োজনে জন চ্যাপম্যান পরিবারসহ আবার লণ্ডনে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। যাবার জন্য স্থির করা দিনটির কয়েকদিন আগের এক সকালে ঘুম ভেঙে অ্যান দেখেন তাঁর খাটের কিনারে কালো মুখের এক লোক দাঁড়িয়ে। পরনে জ্যাকেট, গলায় লাল স্কার্ফ। যখন তার দিকে তাকালেন সে অদৃশ্য হলো। পাশে শুয়ে থাকা জন কিছুই টের পাননি। অ্যান কিছু বলেনওনি।
কয়েকদিন পর দেখা গেল বাড়ির কয়লার মজুত শেষ। চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত বাড়িটা উষ্ণ রাখতে আরও কিছু দরকার। জন বললেন আজ লণ্ডন যাওয়ার পথে অর্ডার দিয়ে যাবেন। পরদিন সকালে অ্যান তাঁকে ধন্যবাদ দিলেন বিষয়টা মনে রাখার জন্য। কিন্তু তিনি জানালেন একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন কয়লার ব্যাপারটা। চাকরদের কেউও কয়লার অর্ডার দেয়নি। অ্যান নিজেই গ্রামে গিয়ে তদন্ত করা স্থির করলেন। কয়লা • ব্যবসায়ী জানাল, সে কয়লা পাঠায় ফ্যাশনেবল জ্যাকেট পরা, গলায় লাল স্কার্ফ জড়ানো এক কালো মুখের তরুণের অর্ডারের প্রেক্ষিতে। সে তাকে না চিনলেও ভেবেছে চ্যাপম্যানদের নতুন কর্মচারী।
যখন সত্যি ভুতুড়ে বাড়িটা ছেড়ে লণ্ডনের নতুন বাড়িতে উঠলেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন মি. এবং মিসেস চ্যাপম্যান’। তখনই জন জানালেন, তিনি খোঁজ নিয়ে জেনেছেন চেস্টনাটের ওই বাড়িটা আসলেই ভুতুড়ে। অসুখী ওই তরুণী মা আর অশুভ নার্স ব্ল্যাকের প্রেতাত্মার কারণে তাঁদের আগে অনেক ভাড়াটেই বাড়িটা ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন।
লণ্ডনের ভূতের রাজ্যে
ইলিয়ট ও’ডনেল একজন গোস্ট হান্টার। ভুতুড়ে বাড়ি বা জায়গার খোঁজে ইংল্যাণ্ডের অনেক এলাকায়ই অভিযান চালিয়েছেন। তাঁর কিছু অভিজ্ঞতা তুলে ধরছি আজ।
সাধারণত ভৌতিক অভিজ্ঞতার কথা বললে আমাদের মনে হয় অভিজাত বাড়ি, ম্যানশন বা পুরানো কোন প্রাসাদের কথা। কিন্তু লণ্ডনের দরিদ্র এলাকাগুলোতেও নানা ধরনের অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটে। যেমন প্যাকহ্যাম রের এক দোকানের কথা বলব এখন।
আগস্টের এক সন্ধ্যা। একটু একটু করে আঁধার হতে শুরু করেছে চারপাশ। দোকানে ঢুকেই চমকে গেলাম। এক মহিলাকে ব্র্যাণ্ডি পান করাচ্ছে দোকান মালিক। মহিলাটি মেঝেতে আধবসা আধশোয়া অবস্থায় আছেন। পুরোপুরি জ্ঞান আছে এটাও বলতে পারব না।
‘হ্যালো, মি. ডি., ঘটনাটা কী?’ জিজ্ঞেস করলাম।
‘মহিলাটি একটু বেশি রকম চমকে গিয়েছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ঠিক হয়ে যাবে।’
বিষয়টা কী জানতে চাইলাম। দোকান মালিক আমার পূর্ব পরিচিত হওয়ায় অমত করল না খুলে বলতে। জানাল যখন বেকন কাটছিল এসময়ই মহিলাটি দোকান থেকে বের হচ্ছিলেন। তারপরই মহিলাটি চিৎকার করে উঠে মূর্ছা যান। তিনি ভেবেছেন দোকান মালিক তার হাতের আঙুল কেটে ফেলেছে।
‘অবশ্য,’ বলল সে, ‘তুমি বলতেই পার এটা একটা হ্যালুসিনেশন কিংবা দৃষ্টিবিভ্রম টাইপের কিছু। তবে এই জায়গার মধ্যে আসলেই অস্বাভাবিক একটা কিছু আছে। সন্ধ্যার একই সময় একই ধরনের ঘটনা দেখার কথা বলেন ক্রেতারা। তাঁরা দেখেন আমার একটা আঙুল কাটা পড়ছে। আশ্চর্য ব্যাপার হলো এটা সবসময় বেকন কাটার সময়ই হয়, চিজ, বিফ কিংবা অন্য কিছু কাটার সময় নয়। বিষয়টা আমার মনের মধ্যে এতটাই চাপ ফেলে যে কখনও মনে হয় সত্যি বুঝি একটা আঙুল কেটে ফেলছি। চিৎকার করে গিন্নিকে ডাকতে শুরু করি।’
‘তাহলে, তোমার স্ত্রী বা অন্য কাউকে বেকনের ব্যাপারটা দেখতে দাও না কেন?’ পরামর্শ দিলাম, ‘তাহলে হয়তো এটা ঘটবে না আর।’
তবে ওটা ঘটল, আরও ভয়ঙ্করভাবে। পরের বার যখন গেলাম তখন ঘটনাটা খুলে বলল সে।
‘জায়গাটা ছাড়ছি আমি। এটা অনেকটাই তোমার কারণে। মনে আছে অন্য কাউকে বেকনের দায়িত্ব দিতে বলেছিলে?’
মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানালাম।
‘তো কাজটা করতে দিই আমার শালীকে,’ বলতে লাগল সে, ‘আমাদের সঙ্গে এসে বাস করার আগে ব্রিক্সটনে একটা রেস্তোরাঁর ব্যবসা ছিল তার। প্রথম রাতে যখন কাজটা করল কিছুই ঘটল না। তবে দ্বিতীয় রাতে তার আতঙ্কিত চিৎকারে দোকানে দৌড়ে যায় আমার স্ত্রী। আমার শালী চিৎকার করে বলছিল, ‘ওহ! আমি আমার আঙুল কেটে ফেলেছি।’ চিৎকারটা আমিও শুনেছি। তবে সেই পুরনো ঘটনা মনে করে পাত্তা দিইনি মোটেই। বরং হাসছিলাম মুচকি মুচকি। কিন্তু তারপরই শালী সিসির ওখান থেকে দৌড়ে কাউন্টারে এসে হাঁফাতে হাঁফাতে আমার স্ত্রী বলল, ‘এখনই একজন ডাক্তারের খোঁজে যাও। ওর আঙুলটা পুরোপুরি কাটা পড়েছে।’’
ক্যানিংটন পার্কের এক বাড়িতেও বেশ অদ্ভুত রকম ভুতুড়ে ঘটনা ঘটে। পুরানো ধাঁচের বাড়িটার থেকে কিছুটা দূরে রাস্তা শুরু হয়েছে।
আমার এক সাংবাদিক বন্ধু, যার রাতের অর্ধেকটা লিখতে লিখতে পার হয়ে যেত প্রায়ই, সেখানে একটা কামরা ভাড়া নিল। তো যে রাতে কামরাটায় উঠল, খুব ক্লান্ত ছিল। হাতে জরুরি কোন অ্যাসাইনমেন্টও ছিল না, তাই একটু তাড়াতাড়িই ঘুমাতে গেল। অন্তত তার হিসাবে। এই কামরাটায় গ্যাস নেই, মোমই ভরসা। একটা মোমকে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে অপরটা নেভাতে যাবে এমন সময় কেমন একটা অস্বস্তি হতে লাগল। বিছানার নিচে তাকাল, ওখানে গিজগিজ করছে তেলাপোকা। এটা তাকে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করল। পৃথিবীতে যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে সে তা হলো এই তেলাপোকা। এক লাফে টেবিলের ওপর উঠে এক পায়ের ওপর আরেক পা আড়াআড়িভাবে রেখে বসে পড়ল। সকাল পর্যন্ত এভাবেই বসে থাকবে স্থির করল।
বেশ কিছুটা সময় বিছানার দিকে তাকালই না। তবে অজানা কোন একটা আকর্ষণে সেদিকে তাকাতে বাধ্য হলো। তখনই বালিশটার দিকে দৃষ্টি গেল। কেমন যেন লাগছে। ভাবল নিশ্চয়ই চোখের কোন সমস্যার কারণে এমনটা হয়েছে। অতএব ঠিক করল, ওদিকে আর তাকাবেই না। কিন্তু আবারও কী এক আকর্ষণে তাকাল ওদিকে। না, কোন ভুল নেই। বালিশটা আর বালিশ নেই, একটা মুখ হয়ে গিয়েছে। ওই তো নাকটা দেখা যাচ্ছে, পুরু আর একটু বাঁকা। কানদুটো বড়, মাথার পেছনের দিকে লেপ্টে আছে। চোখ, মুখ সবই আছে। আর শেষের ওই অঙ্গটাই আমার বন্ধুকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করে। ঠোঁটটা পুরু, মুখটা হাঁ হয়ে আছে। মোটের ওপর বেশ সাধারণ একটা চেহারা। তবে ওটা এখানে কেন?
মোমটা জ্বলতে জ্বলতে ছোট হয়ে এসেছে। পুরোপুরি নিভে যাওয়ার আগেই অপর মোমবাতিটা জ্বেলে ফেলল। আবার মুখটার দিকে তাকাল। বাইরের যান চলাচলের শব্দ একেবারেই থেমে গিয়েছে। ঘোড়ার গাড়ির ঝুনঝুন, ঘোড়ার খুরের আওয়াজ, ট্রামের শব্দ—সব কিছু থেমে গিয়ে আশ্চর্য নীরবতা বিরাজ করছে এখন। তবে এসবে আমার বন্ধুর আগ্রহ নেই। তার সমস্ত মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু যেখানে বালিশটা থাকার কথা এবং এর বদলে ভুতুড়ে মুখটা আছে সেখানটায়।
ধারণা করল, বেশিরভাগ সময়ে বারে কাটানো মদ্যপ এক মোটাসোটা মানুষের মুখ ওটা। ধারণাটা সত্যি করে দিতেই যেন হঠাৎ বিয়ারের গন্ধ নাকে এসে লাগল।
সন্দেহ নেই বাসি বিয়ারের গন্ধ ওটা। আমার বন্ধু যে কিনা এ জিনিস থেকে দূরে রয়েছে সবসময়, তার জন্য গন্ধটা রীতিমত অসহনীয়। এসময়েই কিছু একটা তাকে নিচের দিকে তাকাতে বাধ্য করল। দেখল বিশাল, কালো একটা শুঁড়অলা বস্তু বিছানার চাদর বেয়ে ওপরে উঠছে। ওটার পেছনে আরেকটা, এভাবে একটা একটা করে গোটা চাদরটাই এই বিদঘুটে জীবগুলোয় ভরে গেল। তাদের হাঁটার শব্দও যেন শুনতে পাচ্ছে সে। ওপরে ওঠা জিনিসগুলো গোটা শয্যায়, এমনকী ওই মুখটায় ছড়িয়ে পড়ল। সবার লক্ষ্য ছিল আসলে ওই মুখটাই। বিছানা থেকে জোর করে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল আমার বন্ধুটি। তার এবং দরজার মাঝখানের মেঝের দিকে, দৃষ্টি গেল তার। এখানে-সেখানে কিছু নড়াচড়ার আভাস পেল।
টেবিলে এক হপ্তার ভাড়া রেখে এবং একটা কাগজে বাড়ি ছাড়ার কারণ বর্ণনা করে, আসন থেকে সাবধানে নেমে এল। তারপর ছুটল সামনের দরজার দিকে।
কয়েক হপ্তা পর অন্য একজন পরিচিত সাংবাদিক তাকে জিজ্ঞেস করল, নদীর দক্ষিণ-পুব অংশে একটা কামরার ব্যবস্থা করে দিতে পারবে কিনা, তবে অবশ্যই ক্যানিংটন পার্ক রোডে নয়।
‘কেন নয় সেখানে?’ আমার বন্ধুটি জানতে চাইল।
‘কারণ ওখানে আমার একটা অভিজ্ঞতা। কখনও ভুলব না ওই স্মৃতি। তুমি কি ভূতে বিশ্বাস করো? আর তেলাপোকা নিয়ে কি তোমার কোন দুর্বলতা আছে?
‘কী!’ আমার বন্ধু বিস্ময় প্রকাশ করল, ‘তাহলে ওই বাড়িতেই ছিলে তুমিও!’
তারপর তথ্য চালাচালি হতেই জানা গেল ওই সাংবাদিক যে শুধু ওখানে থেকেছে তা-ই নয় তার অভিজ্ঞতাও অবিকল এক।
‘বাড়ির মালকিনও প্রায়শই ওই কামরার বাসিন্দাদের এই অভিজ্ঞতার ব্যাপারটি জানতেন। সবাই নিশ্চয়ই তোমার মত এতটা উদার ছিল না যে ভাড়াটা পর্যন্ত রেখে আসবে। আর ওই বালিশমুখের ব্যাপারে তুমি কিছু জানো কিনা জানি না। ওই সময় ডাকা এক চিকিৎসকের কাছ থেকে এর বৃত্তান্ত শুনেছি। ওই বাড়ির মালকিন মহিলাটি আসলেই আস্ত এক পিশাচী। কয়েক বছর আগের এক রাতে ওই মহিলার স্বামী এতটাই মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফেরে যে বিছানায় যাওয়ার অবস্থা পর্যন্ত তার ছিল না। বদ মহিলাটি তাকে বিছানায় তুলে শোয়ানোর বদলে রাতভর বিছানার পাশেই ফেলে রাখে। তেলাপোকারা বিয়ার কী পরিমাণ পছন্দ করে তা তো জানো। ওই গন্ধে রীতিমত পাগল হয়ে যায় ওই কামরায় আশ্রয় নেয়া হাজারো তেলাপোকা। সকালে মহিলা এসে দেখে স্বামী দমবন্ধ হয়ে মারা গিয়েছে।
বলা হয় সহো নানা ধরনের প্রেতাত্মার জন্য বিখ্যাত। ডিন স্ট্রিটের এক বাড়িতে বহু বছর ধরে আস্তানা গাড়া একটি বিশাল ভুতুড়ে কালোপাখির কাহিনী বেশিরভাগেরই জানা। তবে গ্রিক স্ট্রিটের এক দোকানের ওপরের ফ্ল্যাটের ঘটনাটা আশা করি পাঠকদের পরিচিত মনে হবে না।
বিশ্বযুদ্ধের পর এক মেডিকেল পড়ুয়া ছাত্র আশ্রয় নেয় গ্রিক স্ট্রিটের ওই বাড়িতে। মোটামুটি হপ্তাখানেক কাটানোর পর একদিন গিয়ে বাড়ির মালকিনকে অভিযোগ করল প্রতিদিন রাতে বিছানাটা শোবার সময় ভেজা পায় সে। মহিলা বলল এটা কোনভাবেই সম্ভব নয়। খেপা ছাত্রটি তখন হুমকি দিল আজ রাতেও একই ঘটনা ঘটলে বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দেবে।
ওই দিন সন্ধ্যায় হাসপাতাল থেকে ফিরতেই মহিলা তাকে বলল তার সঙ্গে কামরায় এসে দেখতে সব কিছু ঠিক আছে কিনা।
‘গোটা বিকালটা রান্নাঘরের আগুনের কাছে রেখেছি তোমার বিছানাটা।’ বলল মহিলা।
মেডিকেল কলেজের ছাত্রটি তার সঙ্গে ভেতরে ঢুকতেই জিজ্ঞেস করল মহিলা, ‘এবার ঠিক আছে তো?’
‘হ্যাঁ, এখন এটা একেবারেই শুকনো। তবে এটা নিশ্চিত গত রাতে ওটা ভেজাই ছিল।’
বেশ রাত করে পড়ালেখা শেষ করে বিছানায় গেল ছেলেটি। কিন্তু যখনই শরীরটা এলিয়ে দিল আবিষ্কার করল ওটা ভেজা। কিন্তু সকালে যখন মহিলাকে দেখাতে নিয়ে যাওয়ার আগে স্পর্শ করে দেখল, অবাক হয়ে আবিষ্কার করল, ওটা একেবারেই শুকনো।
বেশ চমকিত মেডিকেল ছাত্র এবার বাড়ি ছাড়ার নোটিশ দিল। মহিলা তখন তাকে অপর একটা কামরা দিতে চাইল। ছেলেটা এতে কী লাভ হবে বারবার জানতে চাইলে মহিলা অনিচ্ছাসত্ত্বেও জানাল, এই কামরায় আগে যারাই থেকেছে দারি করেছে ওই বিছানাটা ভুতুড়ে।
‘আমি এতদিন একে তাদের কল্পনা ভেবেছিলাম,’ বলল মহিলা; ‘তবে তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে আসলেই কোন সমস্যা আছে। ওই কামরাটার ওপরেই একটা রুম খালি হয়েছে। চাইলে আজই ওটায় উঠে যেতে পার।’ তবে এই ঘটনার পর ছাত্রটির আর ওই বাড়িতে থাকার কোন আগ্রহ ছিল না। সন্ধ্যায়ই সে তল্পিতল্পা গুটিয়ে বিদায় নেয়।
এই মেডিকেল ছাত্রের কথা বলতে গিয়ে উইমপোল স্ট্রিটের কথা মনে পড়ে গেল। ওখানে একটা বাড়িতে প্রায় সময়ই চিকিৎসকরা বাস করেন। ওই বাড়িটারও ভুতুড়ে বলে বদনাম আছে। তবে ওখানকার রহস্যময় অতিথি সাধারণত দেখা দেয় না, বরং শব্দ করে নানা ধরনের। একটা কামরা থেকে চাবুকের শপাং শপাং বাড়ির শব্দ শোনা যেত প্রায়ই। মনে হত যেন কোন মানুষকে কেউ চাবুক দিয়ে ইচ্ছামত পেটাচ্ছে। আবার এক ল্যাণ্ডিঙে বাস করা লোকেরা প্রায়ই প্রচণ্ড হাতাহাতির শব্দ শুনতে পেতেন। শেষ হত কোন একটা কিছু ধপ করে পড়ার শব্দের মাধ্যমে। ধারণা করা হয় ওই বাড়িতে বাস করা কোন ভৃত্য অমানুষিক নির্যাতনের কারণে মারা যায়। তার অতৃপ্ত আত্মাই এই শব্দগুলো ফিরিয়ে আনছে।
যুদ্ধের সময় একেবারেই অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা হয় আমার। উইগমোর স্ট্রিটে এক ভূতের খোঁজে গিয়ে এটা হয়। একটা ফ্ল্যাটে নীল একটা আলো দেখা যায়, এক কামরা থেকে আরেক কামরা চষে বেড়ায় ওটা। আবার প্রতি রাতে একই সময়ে, যখনই আলোটা দেখা যায় একটা ছায়ামূর্তি হাজির হয়। একটা সিঁড়ির নিচে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকে ওটা।
তো এক রাতে আরও কয়েকজন বন্ধুসহ ঠিক করলাম ওই বাড়িটায় ভূতের খোঁজে যাব। রিজেন্ট স্ট্রিটে একটা ক্লাব থেকে কেবল বেরিয়েছি তখনই রাস্তার লাল বাতিগুলো নিভে গেল। তার পর পরই গুলির শব্দের মত দুটো আওয়াজ।
সবাই নিরাপদ আশ্রয়ে সরে পড়ল। কিন্তু আমি ওই বাড়িটায় হাজির হওয়ার জন্য লাফ দিয়ে একটা বাসে উঠে পড়লাম। অক্সফোর্ড সার্কাসে আমাকে ছাড়ল বাসটা। উইগমোর স্ট্রিটে যখন এলাম তখন দেখলাম রাস্তায় আমিই একমাত্র পথচারী। তারপরই রীতিমত বিশৃঙ্খল আর ভয়ানক একটা পরিস্থিতি তৈরি হলো। রাস্তা ও ফুটপাতের ওপর গোলার টুকরো পড়তে লাগল। বেশ বিচলিত হয়ে পড়লাম। মাথায় কেবল নরম ফেল্ট টুপি আমার। চারপাশে ঘন অন্ধকার, কেবল একটা ল্যাম্প পোস্ট থেকে লাল একটা আলো আসছে। এসময় কটা নীল আলো চোখে পড়ল। ওই আলোয় ফুটে উঠল অশুভ কটা শব্দ, ‘তাড়াতাড়ি নিরাপদ কোথাও গা ঢাকা দাও।’
সত্যি ভয় পেলাম। এক ছুটে ভুতুড়ে বাড়িটাতে গিয়ে উঠলাম। বাড়ির মালিক মহিলা আর তার সঙ্গী ছাড়া আর কেউ নেই। আমার যে বন্ধুদের জন্য ঝুঁকি নিলাম তারা একজনও আসেনি। রাতভর সেখানে থেকেও কোন ধরনের অস্বাভাবিক আলামত পেলাম না। ‘সম্ভবত গোলাগুলির শব্দ ওটাকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ। অন্যান্য সাবধানী নাগরিকদের মত গা ঢাকা দিয়েছে সে-ও।’ ঠাট্টা করে বললেন ভদ্রমহিলা।
হারলে স্ট্রিটের দুটো বাড়ির কথা জানি সেগুলো ভুতুড়ে। এই এলাকায় একসময় চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানীদের গবেষণার প্রয়োজনে অনেক কুকুরকেই যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে বলে শুনেছি। একটা বাড়িতে যেমন একটা স্প্যানিয়েল কুকুরের অশরীরীকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। ওটার প্রচণ্ড যন্ত্রণায় চিৎকার করার শব্দ শুনলে শরীরের রোম দাঁড়িয়ে যাবে আপনার। এদিকে অপর একটা বাড়িতে, অর্ধ শতাব্দী আগে যেখানে ভয়ানক একটা অপরাধ সংঘটিত হয়, সেখানে অশরীরী হাজির হয় একটা পিপের বেশে, থপ থপ শব্দ করতে করতে কিচেনের সিঁড়ি বেয়ে ওটা নেমে যায় পাতালঘরের দিকে।
ডোভার স্ট্রিটের কাছে একটা দোকানের ওপরে একটা ফ্ল্যাট নিয়েও নানা ধরনের কিচ্ছা প্রচলিত। বেশ কয়েক বছর আগে এক ব্যারিস্টার বন্ধুসহ সেখানে হাজির হলাম। তবে ফ্ল্যাটটায় রাত কাটানোর অনুমতি পেলাম না। খুব নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানতে পারলাম, এক নারী রাতে কেউ শুয়ে থাকলেই ওই বিছানায় গিয়ে বসে। ওই সময় শুয়ে থাকা ব্যক্তিটি গলায় প্রচণ্ড চাপ অনুভব করতে থাকে। কখনও কখনও মূর্ছাও যায়। এর নির্ভরযোগ্য কোন ব্যাখ্যা পাওয়া না গেলেও একটা তত্ত্ব বেশ ডালপালা মেলেছে। একসময় ফ্ল্যাটটায় অর্ধ-উন্মাদ এক নারী বাস করত। সে নিজের বোনকে এবং তারপর নিজেকেই গলা টিপে মেরে ফেলে। অবশ্য আমার গবেষণায় বহু আগেই বেরিয়ে এসেছে, যেসব বাড়িতে এ ধরনের উন্মাদরা বাস করেছে এবং এভাবে গলা টিপে কাউকে মেরেছে, সে বাড়িগুলোতে এ ধরনের গলা চেপে ধরার অভিজ্ঞতা হয় লোকেদের মাঝে মাঝেই।
এতক্ষণ ভুতুড়ে বাড়ি নিয়ে পড়ে থাকলেও এবার ব্রিজের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন কয়েকটা ভুতুড়ে ঘটনা দিয়ে এই অধ্যায়টি শেষ করতে চাই। টেমস নদীর সঙ্গে এত বেশি খুন, আত্মহত্যা এবং দুর্ঘটনার সম্পর্ক আছে যে এর দু’তীরে ভুতুড়ে ঘটনা ঘটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।
বাঁধ আর কোন কোন সেতুতে দেখা যাওয়া ভূতেদের কথা বলছি। রাতে এখান দিয়ে চলাফেরা করা পথচারী, ভবঘুরে আর রিভার পুলিসদের এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয়। এদের কাছ থেকেই ওখানকার অশরীরীদের সম্পর্কে জানতে পারি আমি
জীবন সম্পর্কে হতাশ এক ভবঘুরে আমাকে বলল এক রাতে ওয়াটার লু সেতুর ওপর দিয়ে নদীর দিকে ঝুঁকে ছিল, লাফ দেয়ার সাহস সঞ্চয় করার জন্য। এসময় টলতে টলতে এক সুবেশী যুবক তাকে পাশ কাটাল। মনে হচ্ছে আকণ্ঠ মদ খেয়েছে। যুবকের সঙ্গের সোনার ঘড়ি আর হারটা ওই ভবঘুরেকে লোভী করে তুলল। আত্মহত্যার চিন্তা বাদ দিয়ে তাকে অনুসরণ শুরু করল সে। একপর্যায়ে সেতুর পাশে পাঁচিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেটাকে ভারসাম্য রক্ষা করতে দেখে খুশি হয়ে উঠল ভবঘুরে। চমৎকার একটা সুযোগ চলে এসেছে। চুপিসারে তার পেছনে এসে হাত বাড়াল ঘড়িটা টান দেয়ার জন্য। কিন্তু হাত কিছুই পেল না। পরমুহূর্তে ভারসাম্য হারিয়ে জোরে বাড়ি খেল দেয়ালের সঙ্গে। কিন্তু তার শিকারের কোন দেখা নেই। যেন বা সেতুটা হঠাৎ ফাঁক হয়ে তাকে অতলে টেনে নিয়েছে।
ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজে ভুতুড়ে এক অভিজ্ঞতার কথা আমাকে বলে এক পুলিস সদস্য। অ্যাবির দিক থেকে রাত দুটোর দিকে সেতু পেরোচ্ছিল সে। এসময়ই মনে হলো তার পেছনে কেউ দৌড়চ্ছে। ঘুরতেই সুন্দরী, দামি পোশাক পরা এক মেয়ের মুখোমুখি হয়ে গেল।
‘দয়া করে আমার সঙ্গে এসো। এই মাত্র এমন একজনকে রেখে এসেছি, যে খুব বিপদে আছে।’ আর্তি জানাল মেয়েটা।
সার্জেন্টকে তখনই রিপোর্ট করার কথা থাকায় পুলিসটা দ্বিধা করছিল। তবে মেয়েটা এমন করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল যে সে তাকে অনুসরণ করতে বাধ্য হলো। বাঁধের কোনায় আসতেই দেখল একটা মেয়ে নদীতে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছে। বেশ জোর-জবরদস্তি করে মেয়েটাকে নিচে নামাতে পারল। তার মুখের দিকে তাকাতেই ধাক্কা খেল। যে মেয়েটা তাকে ডেকে নিয়ে এসেছে সে দেখতে অবিকল তারই মত। একটা ব্যাখ্যা পাওয়ার আশায় পেছনে তাকাতেই দেখল পথ প্রদর্শক মেয়েটি গায়ের হয়েছে।
‘তোমার বোন, আরও পরিষ্কারভাবে বললে যমজ বোনটি ‘গেল কই?’ আত্মহত্যার চেষ্টাকারীর দিকে চেয়ে চিৎকার করে
বলল পুলিসটি। চারপাশে খুঁজছে সে ওই মেয়েটিকে।
‘কার কথা বলছ?’ প্রাণ দিতে যাওয়া মেয়েটা বলল।
‘কেন, তোমার যমজ বোন। যে আমাকে ডেকে এনেছে তোমার আত্মহত্যা ঠেকাতে।’
‘কী বলছ এসব,’ এবার অবাক হবার পালা মেয়েটির, ‘পাগল নাকি? আমার যমজ বোন তো দূরে থাক কোন বোনই নেই। আমার কোন বন্ধু নেই, স্বজন নেই, আমি একেবারেই একা। এখানে আসার পর কোন মেয়েকে দেখিনি, এ ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিতে পারি।’
বেলেচিনের প্রেতাত্মারা
স্কটল্যাণ্ডের বেলেচিন হাউসের অবস্থান ছিল লজিয়েরেট থেকে কয়েক মাইল দূরে পাহাড়ি এলাকায়। টে নদীর উপত্যকার ওপর ঝুলে ছিল অনেকটা। বিচিত্র সব স্পিরিটের কারখানা হিসাবে পরিচিতি পাওয়া ডানকেলডও ওখান থেকে খুব দূরে নয়।
স্টুয়ার্ট পরিবার ষোলো শতক থেকেই এস্টেটটার মালিক। রাজা দ্বিতীয় রবার্টের বংশধর ছিল স্টুয়ার্টরা। পুরানো ম্যানর হাউসের বদলে বেলেচিন হাউস তৈরি হয় ১৮০৬ সালে।
যাঁর মাধ্যমে বেলেচিন হাউসে ভুতুড়ে কাণ্ড-কারখানার সূচনা তিনি রবার্ট স্টুয়ার্ট। বেলেচিন হাউসটা যখন বানানো হয় তখনই তাঁর জন্ম। ১৮২৫ সালে উনিশ বছর বয়সে ভারত যান রবার্ট, সেখানে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীর একজন অফিসার হিসাবে যোগ দেন। পঁচিশ বছর পর মেজর হিসাবে অবসরে যান। বাবার মৃত্যুর পর ১৮৩৪ সালে বেলেচিনের উত্তরাধিকারী হন তিনি। ১৮৫০ সালে যখন ভারত থেকে ফেরেন আবিষ্কার করেন তাঁর বাড়িটায় ভাড়াটেরা থাকছে। বেলেচিন কটেজ নামে এস্টেটের সীমানার মধ্যে ছোট্ট এক কটেজ তৈরি করান তিনি। সেখানে ভাড়াটেদের চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত থাকেন। তারপর মূল বাড়িতে ওঠেন।
মেজর স্টুয়ার্ট ছিলেন একটু খোঁড়া। ধারণা করা হয় ভারতে দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে কোন এক দুর্ঘটনায় জখম হন তিনি। অবিবাহিত ছিলেন। তবে তরুণী এক হাউসকিপার সবসময় সঙ্গ দিত তাঁকে। দু’জনের সম্পর্ক নিয়ে নানান কানাঘুষা শোনা যায়। তাঁর ছিল দুই ভাই এবং ছয় বোন। বোনদের একজন ইসাবেলা সন্ন্যাস জীবন বেছে নেন। বাড়ির অশরীরী কাজ-কারবারের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্রে পরিণত হন পরে এই নারী। ১৮৮০ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি এক আশ্রমে মৃত্যু হয় তাঁর।
১৮৭৬ সালে মারা যাওয়া মেজর স্টুয়ার্ট ছিলেন খুব খামখেয়ালি মানুষ। ভারতে অতিপ্রাকৃত বিষয়ের প্রতি আগ্রহ জাগে তাঁর। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন মারা যাওয়ার পর আত্মা অন্য কিছুতে ভর করে ফিরে আসতে পারে। বেলেচিনে যে পঁচিশ বছর বাস করেন অদ্ভুত আচার- আচরণের জন্য গোটা জেলায় রীতিমত পরিচিত হয়ে যান।
গোটা বাড়িটা নানা ধরনের কুকুর দিয়ে ভরিয়ে ফেলেন তিনি। তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ছিল একটা বিশাল কালো স্প্যানিয়েল। মৃত্যুর পর ওটার দেহেই ফিরে আসার বাসনা ছিল স্টুয়ার্টের। মেজর স্টুয়ার্টের কুকুরের দেহে ফিরে আসার এই খায়েশ তাঁর বংশধর ও আত্মীয়-স্বজনরা মোটেই সহজভাবে নেয়নি। রবার্ট স্টুয়ার্টের মৃত্যুর পর দেরি না করে স্প্যানিয়েলটাসহ সবগুলো কুকুরকেই গুলি করে মারে তারা। ধরে নেয় এভাবে মেজরের ফিরে আসার পথ বন্ধ হয়ে গেল।
১৮৫৩ সালের উইলে মেজর বেলেচিনের উত্তরাধিকার করেন তাঁর বিবাহিত বোন মেরির সন্তানদের। মেরির ছিল পাঁচ সন্তান। ১৮৬৭ সালে বড় ছেলে মারা যান। পরের বছরই ছোট তিন সন্তানকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করে নতুন উইল করেন। এতে ১৮৭৬ সালে বেলেচিনের একমাত্র মালিক বনে যান মেরির দ্বিতীয় পুত্র জন। দেরি না করে নিজের নামের সঙ্গে স্টুয়ার্ট জুড়ে দেন। সরাসরি উত্তরাধিকার না হওয়া সত্ত্বেও বংশ ঐতিহ্য ঠিক রাখার জন্য এটা করেন বলে ধারণা করা হয়।
খালা ইসাবেলার মত জন স্টুয়ার্ট ছিলেন ক্যাথলিক খ্রীষ্টান। বুড়ো মেজর ছিলেন একজন প্রটেসট্যান্ট। লজিয়েরেটের গোরস্থানে ২৭ বছর বয়সী তাঁর সেই হাউসকিপারের পাশেই সমাহিত করা হয় তাঁকে। ১৮৭৩ সালে রহস্যময়ভাবে মারা যায় সারা নামের ওই মেয়েটি।
বেলেচিনের প্রধান বেডরুমে মৃত্যু হয় সারার। পরবর্তীতে বাড়ির সবচেয়ে ভুতুড়ে কামরায় পরিণত হয় এটি। যে বিছানায় সারা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তার চারপাশে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মেজরের ভূতের চলাফেরা করার আওয়াজ পাওয়া যেত।
জীবিত থাকা অবস্থায় একুশ বছর মামার ওই সম্পত্তির আয়-রোজগারে আরামের সঙ্গেই দিন গুজরান করেন জন স্টুয়ার্ট। বিবাহিত ছিলেন তিনি, কয়েকটা সন্তানও ছিল। বড় ছেলে যোগ দেয় সেনাবাহিনীতে, ছোটটা হয় যাজক। জন স্টুয়ার্টের সময় মামার গড়ে তোলা ওই কটেজটায় নান বা সন্ন্যাসিনীদের থাকার ব্যবস্থা হয়। ওই সময়ই ভুতুড়ে ঘটনার শুরু।
বুড়ো মেজরের মৃত্যুর পর পরই তাঁর ভাগ্নে বউ মিসেস স্টুয়ার্ট, যে কামরাটাকে মেজর স্টাডি হিসাবে ব্যবহার করতেন সেখানে নিজের বিভিন্ন জিনিসপত্র রাখা শুরু করেন। এসময়ই একদিন হঠাৎ কামরাটায় কুকুরের কড়া গন্ধ পেতে থাকেন। ছোট্ট ডেস্কটায় বসে কুকুরের গায়ের গন্ধ কীভাবে এল এটা ভেবে বের করার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর মনে পড়ল যখন মেজরের মৃত্যুর পর সবগুলো কুকুরকে পরপারে পাঠিয়ে দেয়া হয় তখনও কামরাটায় এমন একটা গন্ধ পাওয়া গিয়েছিল। তারপরই সবচেয়ে বড় ভয়টা পেলেন। মনে হলো, অদৃশ্য একটা কুকুর ধাক্কা দিচ্ছে তাঁকে। তাঁর মনে হলো কুকুরগুলোকে মেরেও মেজরের অতৃপ্ত আত্মার হাজির হওয়া বন্ধ করতে পারেননি তাঁরা।
এদিকে মেজরের মৃত্যুর পর থেকে কিছু রহস্যময় ঘটনা ঘটতে থাকে। বিভিন্ন কামরায় জোরে টোকা দেয়ার শব্দ শোনা যায় যখন-তখন। নানা ধরনের অদ্ভুত আওয়াজ হয়। হঠাৎ একটা কামরার মাঝখান থেকে শোনা যেতে থাকে ঝগড়ার শব্দ।
চাকর-বাকরেরা আর এখানে থাকতে রাজি হলো না। তাদের মাধ্যমে গল্পগুলো ছড়িয়ে পড়ল আশপাশের এলাকায়। একপর্যায়ে স্কটল্যাণ্ডের সবচেয়ে ভুতুড়ে বাড়ির তকমা লেগে গেল এর গায়ে।
১৮৭০-এর দশকের শেষ দিকে স্টুয়ার্টদের সন্তানদের দেখভালের দায়িত্বে থাকা গভর্নেস মেয়েটাও একের পর এক ভুতুড়ে ঘটনা এবং অস্বাভাবিক শব্দের জন্য চাকরি ছেড়ে চলে যায়। এ বাড়িতে কিছুদিন বাস করা এক যাজক বলেন তাঁর বিছানা এবং ছাদের মাঝামাঝি কোন জায়গা থেকে বিস্ফোরণের মত একটা শব্দ হতে থাকে টানা।
কটেজে বাস করা সন্ন্যাসীদের আত্মিক প্রশিক্ষণের জন্য বেলেচিনে আনা হয় ফাদার হেইডেনকে। বাড়ির মালিককে সমস্যার বিষয়টা খুলে বলেন তিনি। জন স্টুয়ার্ট অনুমান করেন তাঁর প্রয়াত মামার কীর্তি এটা। মেজরের পৃথিবীতে ফিরে আসবার জন্য প্রার্থনা করবেন এই আশায় যাজকের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করছেন তিনি।
যাজক আরও বেশ কিছু অতিপ্রাকৃত ঘটনা টের পান। বিশেষ করে বড় একটা জানোয়ারের চিৎকার, সম্ভবত কোন কুকুরের। বাইরে থেকে তাঁর ঘরের দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার শব্দও পেতেন তিনি। কখনও দরজায় টোকা দেয়ার ঠক ঠক আওয়াজও শুনতেন যাজক।
স্টুয়ার্ট পরিবার বেশ চিন্তিত হয়ে পড়ল। বিশেষ করে ছোট ছেলে-মেয়েদের কথা ভেবে। জন স্টুয়ার্ট নিজেও একদিন এক জানালা থেকে ভুতুড়ে কয়েকজন সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনীকে দেখেন। এদিকে ফাদার হেইডেন যে কামরায় থাকতেন পরে এক রাতে ওই কামরায় ঘুমানো এক দম্পতিও একই ধরনের অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন। একপর্যায়ে স্টুয়ার্ট বেলেচিন হাউসের কিছু অংশ সম্প্রসারিত করে মোট ১২টি নতুন বেডরুম তৈরি করান। উদ্দেশ্য, অন্তত ছেলে- মেয়েগুলো যেন দালানের ভুতুড়ে অংশের বাইরে থাকে।
জানুয়ারি ১৮৯৫ সালে ঘটে ভয়ানক ঘটনাটা। এক সকালে পারিবারিক এক ব্যবসার কাজে লণ্ডনের উদ্দেশে রওয়ানা দেয়ার কথা তাঁর। স্টাডিতে এজেন্টের সঙ্গে কথা বলছিলেন। এসময় হঠাৎ প্রবল তিনটি টোকার শব্দে কথা থামিয়ে দিতে বাধ্য হন দু’জনে। ওই দিন লণ্ডনে পৌছার পরই গাড়ি চাপায় মারা যান জন স্টুয়ার্ট। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে ওই টোকার শব্দের কোন ভূমিকা আছে কিনা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল।
বেলেচিনের পরবর্তী স্টুয়ার্ট ছিলেন এক আর্মি ক্যাপ্টেন। তবে এই ভুতুড়ে বাড়িতে বাস করার কোন ইচ্ছাই তাঁর ছিল না। বিশাল এস্টেটটাকে ১৮৯৬ সালে একটা ধনী পরিবারের কাছে ভাড়া দিতে মোটেই বেগ পেতে হলো না তাঁর।
তবে ক্যাপ্টেন পরিবারটির কাছে বাড়িটার ভুতুড়ে বলে যে বদনাম আছে তা প্রকাশ করেননি। অগ্রিম ভাড়া দিয়ে এক বছরের জন্য এস্টেটটার অধিকার পায় পরিবারটি। মাত্র সাত সপ্তাহ এখানে কাটাতে সমর্থ হয়। রাত্রিকালীন নানা উপদ্রব এবং শরীরের রক্ত পানি করে দেয়া ভুতুড়ে কুকুরের গর্জন তাদের এলাকাছাড়া হতে বাধ্য করে।
বিছানার চারপাশে একটা খোঁড়া লোকের চলার শব্দে ভয় পেয়ে বাড়ির মেয়েটা ভাইকে ডেকে আনে। সে কামরার মধ্যে সোফায় শুয়ে পড়ে। শুতে না শুতেই ওই খোঁড়ানো পদশব্দ শুরু হয় আবার। ছেলেটা নিশ্চিত হয়ে যায় বোনের বিছানার চারপাশে কেউ খুঁড়িয়ে হাঁটছে। তবে দু’জনের কেউই কাউকে দেখতে পায়নি। ১৮৭৩ সালে এই বিছানায়ই মারা যায় সারা। তবে ভাইটি পরে দু’বার এক অশরীরীকে দেখার দাবি করে। একবার একটা ঘন, দুর্ভেদ্য কুয়াশার আবরণে ঢাকা অবস্থায়, দ্বিতীয়বার ওটা হাজির হয় একটা লোকের বেশে। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢোকে, তবে দেয়ালের সামনে গিয়ে অদৃশ্য হয়।
১৮৯৬ সালের সেপ্টেম্বরটা ছিল বেলেচিনের জন্য বিভীষিকাময়। ওই সময় অতিথি হিসাবে থাকা এক নারী লেখেন, প্রতি রাতে প্রবল ঠক ঠক শব্দ, আর্ত চিৎকার আর গোঙানিতে চমকে উঠতে হত বাড়িসুদ্ধ লোককে। অতিথিরা দরজায় প্রবল ধাক্কার শব্দে জেগে উঠতেন। মনে হত দরজাটাই ছিটকে পড়বে। কিন্তু সাহস করে দরজা খুললে কাউকেই পেতেন না। এমনকী একটা কামরায় কুকুর পর্যন্ত থাকতে চাইত না কোনভাবেই।
দ্য টাইমসের ১৮৯৭ সালের ৮ জুন সংখ্যায় এই বাড়ির ভুতুড়ে কাণ্ড-কারখানাগুলো নিয়ে একটি নিবন্ধ ছাপা হয়। তারপর সেখানে ছাপা হয় বেলেচিনের প্রাক্তন বাটলার হেরল্ড স্যাণ্ডার্সের একটি চিঠি। স্যাণ্ডার্স বাড়ির সবাইকে আতঙ্কিত করে তোলা ভয়ানক এক গর্জনের কথা বলে। তারপরই বাড়ির চাকর-বাকরেরা বিদায় নেয়। এমনকী বাড়িতে বেড়াতে আসা অতিথিরা রাতে ভয়ে লাঠি আর রিভলভার নিয়েও জেগে কাটান।
এদিকে এখানকার অশরীরীদের হানা দেয়ার বিষয়টি অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে কাজ করা গোস্ট হান্টারদের নজর কাড়ে। এদের মধ্যে আছেন কর্নেল টেইলর এবং মিস গুডরিচ ফ্রিয়ার। টেইলর অল্প সময়ের জন্য স্টুয়ার্ট পরিবারের কাছ থেকে ভাড়া নেন বাড়িটা।
টেইলর কোন কারণে যেতে না পারায় বান্ধবী মিস কন্সটেন্সি মুরসহ ১৮৯৭ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি বেলেচিনে আস্তানা গাড়েন মিস ফ্রিয়ার।
সেদিন তুষার পড়ছিল অঝোর ধারায়। বাড়িটাকে মনে হচ্ছিল অশুভ। মিস ফ্রিয়ার তাঁর জার্নালে লেখেন, ‘একটা ভল্টের মত মনে হচ্ছিল ওটাকে। কয়েক মাস যাবৎ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল ওটা। যেসব জিনিসপত্রের অর্ডার দিয়েছিলাম একটাও এসে পৌছেনি। আমাদের ছুরি, প্লেট, ওয়াইন কিছুই ছিল না। খাবার আর জ্বালানী ছিল নামকাওয়াস্তে। লজিয়েরেট থেকে আসার সময় সঙ্গে আনা রুটি, মাখন এবং টিনের মাংস খেয়ে বিছানায় যাই। কামরাটা ছিল অসম্ভব শীতল।’
আগের দিনের পরিশ্রমের কারণে মড়ার মত ঘুমাচ্ছিলেন দু’জনে। রাত তিনটার দিকে চড়া একটা শব্দে ঘুম ভেঙে যায় তাঁদের। সাড়ে চারটার দিকে বেশ কয়েকটি কণ্ঠের কথা বলার আওয়াজ পান। তবে সকালে অবশ্য সব ধরনের অস্বাভাবিক শব্দ থেমে যায়। পরের দিন রাতে তাঁরা জোরে জোরে কিছু আবৃত্তি করার শব্দ শুনতে পান, অনেকটা কোন যাজকের ধর্মগ্রন্থের শ্লোক পড়ার মত।
পরবর্তীতে তাঁদের এখানকার অনুসন্ধানের বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ পায় দ্য এলিজড হণ্টিং অভ বি. হাউস নামে। তবে ছদ্মনাম ব্যবহার করার কারণে অনেকেই তখন বুঝতে পারেননি কোন্ বাড়িটার কথা বলা হচ্ছে। ১৮৯৯ সালে প্রকাশিত হয় বইটি।
মিস ফ্রিয়ার নানের অশরীরীকে বরফে ঢাকা বার্নের কাছে কয়েকবার দেখেছেন। প্রথমবার এক নিঃসঙ্গ নান কাঁদছিল বিরামহীন। অন্য সময় নানা ছিল দু’জন। একজন হাঁটুতে ভর দিয়ে কাঁদছিল, অপরজন মৃদুস্বরে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছিল। ধারণা করা হয় এই নানরা জন স্টুয়ার্টের সময়কার, যখন ছোট কটেজটায় নানরা বসবাস করত। তবে এটাও হতে পারে কাঁদতে থাকা সন্ন্যাসিনীটি আর কেউ নন, ইসাবেলা, ১৮৮০ সালে এক আশ্রমে যিনি মারা যান।
তবে সব কিছু মিলিয়ে দেখা যায় মোটামুটি তিন ধরনের অতিপ্রাকৃত ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু বাড়িটি।
প্রথমত, দুই নান। ইসাবেলার বরফঢাকা বার্নের পাশে কাঁদার রহস্য কী?
দ্বিতীয়ত, সারার রহস্যময় মৃত্যুর কারণে স্টুয়ার্টের খোঁড়া ভূতের নারীটির বিছানার চারপাশে হাঁটা।
তৃতীয়ত, মেজরের প্রিয় কালো স্প্যানিয়েল। যার শরীরে বাস করতে চেয়েছিলেন মেজর মৃত্যুর পর। এটা এড়ানোর জন্য স্টুয়ার্টের বংশধরেরা ওটাসহ অন্য কুকুরগুলোকে নির্দয়ভাবে গুলি করে মারে।
মৃত প্রাণীদের ভূতের অনেক গল্প শোনা গেলেও এটা অনেক বেশি বাস্তবসম্মত। প্রথমে এর কথা বলেন মিসেস স্টুয়ার্ট। পরের বিশ বছর অনেক মানুষই অদৃশ্য একটা কুকুরের পায়ের শব্দের উল্লেখ করেন। প্রায়ই কোন কুকুরের দরজার ওপর লাফিয়ে পড়ার আওয়াজও পাওয়া যেত। একটা ভয়াবহ অভিজ্ঞতা ঘটে মিসেস ফ্রিয়ারেরই। তাঁর বিছানায় ওই রাতে শুয়ে ছিল স্পোকস নামের একটা কুকুর। ওটা ছিল ১৮৯৭ সালের ৪ মে। মধ্যরাতে জন্তুটার ভয়াবহ গোঙানির শব্দে ঘুম ভেঙে যায় মিস ফ্রিয়ারের। মোম জ্বালতেই দেখেন স্পোকস ভয়ার্ত দৃষ্টিতে বিছানার পাশের টেবিলের দিকে তাকিয়ে আছে। ওই দৃষ্টি লক্ষ্য করে তাকাতেই টেবিলের ওপর কেবল এক জোড়া কালো পা দেখলেন। ওপরে কিছু নেই। ‘অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলাম ওই দৃশ্য দেখে।’ স্মৃতিচারণ করেন ফ্রিয়ার।
এমনকী এই বাড়িতে বাস করা বেশ যুক্তিবাদী মেইডরাও তাদের ভুতুড়ে সব অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিয়েছে। রান্নাঘরের দায়িত্বে ছিল লিজি। সে জানায় তার বিছানার চাদরটা অদৃশ্য এক জোড়া হাত ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। ওপরতলার মেইড কার্টার জানায় এক ভোরে ঘুম থেকে জেগে দেখে ধূসর শাল পরা এক নারীর অর্ধেক শরীর তার বিছানার পাশে। ওই অশরীরীর কোন পা ছিল না। পুরোপুরি আলো হওয়া পর্যন্ত কম্বলের ভেতর কাঁপতে থাকে মেয়েটা। তারপর এক ছুটে বাড়িতে। আর কখনও বেলেচিনমুখী হয়নি।
শেষ পর্যন্ত বেলেচিন হাউস স্টুয়ার্টদের হাতছাড়া হয়। ১৯৩২ সালে মি. আর. ওয়েমিস হানিম্যান নামের এক ভদ্রলোক এটা কিনে নেন। ১৯৬৩ সালে ভেঙে ফেলা হয় পুরানো বাড়িটি।
প্রেতাত্মার প্রতিশোধ
১৭৫৫ সালের গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যা। ক্যাম্পবেল অভ ইনভেরাওয়ি ক্রুচানের পাহাড়ি পথে হাঁটছিলেন। এসময়ই একজনকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে দেখলেন। বেশ দ্রুতগতিতে আসছে সে, তবে একই সঙ্গে টলমল করছে। দৃশ্যটা দেখে ইনভেরাওয়ির জমিদারের কৌতূহল হলো। পাহাড় বেয়ে নেমে এলেন লোকটার সঙ্গে মিলিত হতে।
কাছাকাছি আসতেই ইনভেরাওয়ি (নিজেও জায়গাটির নামেই পরিচিত ছিলেন) বুঝতে পারলেন লোকটার এই অস্বাভাবিকতার কারণ। শুধু যে ক্লান্ত তাই না, বেশ আহতও। চোখ-মুখে আতঙ্কের ছাপ সুস্পষ্ট। আক্রান্ত হতে পারে এই ভেবে জমিদারের পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল লোকটি। ‘স্যর, দয়া করুন। এই বিপদ থেকে বাঁচান।’
‘শান্ত হও,’ বললেন তিনি, ‘আমার কাছে তুমি নিরাপদ। কী হয়েছে বলো। তোমার এই করুণ হাল হলো কীভাবে? আশা করি সাহায্য করতে পারব তোমাকে।’
বিধ্বস্ত লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, ‘ওরা আমার পিছু নিয়েছে।’ কেঁদে উঠল সে, ‘রক্তের বদলা নিতে আমাকে অনুসরণ করে আসছে। স্যর, হাতে সময় নেই একেবারেই। আমাকে দেখা মাত্র খুন করবে। দয়া করুন।’
ইনভেরাওয়ির ক্যাম্পবেলের লোকটার মর্মান্তিক অবস্থা দেখে দয়া হলো। ‘আমি তোমাকে বাঁচাব। প্রতিজ্ঞা করছি। ইনভেরাওয়িরা কখনও কথা দিয়ে তা রাখতে ব্যর্থ হয় না।’
তারপর আগন্তুককে ক্রুচান পাহাড়ের একটা গোপন গুহায় নিয়ে চললেন। এর খোঁজ কেবল তিনিই জানেন। যুগের পর যুগ ধরে গুপ্ত এই স্থানটার খবর দাদা থেকে বাবা, বাবা থেকে ছেলে এভাবে জেনে আসছে। পুরানো দিনে অনেক যোদ্ধাই এটিকে লুকানোর জায়গা হিসাবে ব্যবহার করেছিলেন। প্রবেশ পথটা এতটাই ছোট যে পথচারীরা দেখলে ভাববে শিয়ালের গুহা। ভেতরে বেশ কয়েকটা বড় কুঠুরী আছে। এর একটায় আবার ঝরনার জল জমে একটা কুয়ার মত তৈরি হয়েছে।
লোকটাকে গুহার কাছে পৌঁছে দিয়ে ইনভেরাওয়ি চলে যাবার জন্য উদ্যত হলেন। কিন্তু লোকটা তাঁর হাত চেপে ধরে তাকে একা রেখে চলে না যাওয়ার জন্য কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। এত ভীতু একটা লোককে সাহায্য করার শপথ করেছেন বলে মেজাজ খিঁচড়ে গেল জমিদারের। বেশ কিছুটা অসন্তুষ্ট কণ্ঠেই বললেন, ‘আর একটু সাহসী হওয়ার চেষ্টা করো। এখানে তুমি নিরাপদ। তোমার পিছু নিয়েছে যারা, জায়গাটা খুঁজে পাবে না। পরে খাবার নিয়ে আসব তোমার জন্য।’
আগন্তুক শান্ত হলো। বিড়বিড় করে ধন্যবাদ জানাল জমিদারকে। তারপর পাহাড়ের এবড়ো-খেবড়ো পথ ধরে তাঁর শরীরটা অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল।
ইনভেরাওয়ি যখন প্রাসাদে পৌঁছলেন দেখলেন একজন লোক অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য। লোকটাকে খুব অস্থির দেখাচ্ছে। বার্তাবাহক জানাল খারাপ একটা সংবাদ নিয়ে এসেছে সে। ইনভেরাওয়ির মনে হলো তাঁর পালক ভাইয়ের সঙ্গে নিশ্চয়ই এর সম্পর্ক আছে। তাকে বড্ড ভালবাসেন তিনি। কী শুনতে হয় ভেবে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন মনে মনে। ‘স্যর, মেচনিভেন নামের এক লোক নৃশংসভাবে আপনার পালক ভাইকে হত্যা করেছে,’ বলল লোকটা। ‘খুনেকে অনুসরণ করে এই জায়গাটির মোটামুটি কাছাকাছি চলে আসি আমরা,’ বলতে লাগল বার্তাবাহক। ইনভেরাওয়ি জায়গাতেই যেন জমে গেলেন। একটা বিষয় পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে তাঁর কাছে। ‘আমি এখানে এসেছি আপনাকে সতর্ক করতে, যদি লোকটা আবার আপনার কাছে সাহায্য চেয়ে বসে।’
ফ্যাকাসে চেহারা নিয়ে ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ এবং তার হত্যাকারীকে ধরার যে চেষ্টা চালানো হচ্ছে তা শুনলেন ইনভেরাওয়ি। বার্তাবাহক ভাবল, পালক ভাই হারানোর শোকে এতটাই মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন তিনি যে কথা বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছেন। তাঁকে একা থাকার সুযোগ দিয়ে পলাতক খুনিটাকে ধরার অভিযানে যোগ দেয়ার জন্য ছুটল সে।
একা হতেই ইনভেরাওয়ির মাথায় এল, এখন তিনি কী করবেন? শুধু যে খুনিটাকে সাহায্য করেছেন তা নয় তাকে রক্ষা করার শপথও করেছেন। তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে কাপুরুষ মেচনিভেন যা করেছে তা ফিরিয়ে দেয়ার প্রবল একটা ইচ্ছা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তাঁকে কথা রাখতে হবে। কিন্তু নিজেকে শান্ত করে কিছু খাবার নিয়ে গুহার দিকে চললেন। মেচনিভেনকে খাবারটা পৌঁছে দিয়ে আগামীকাল আরও খাবার নিয়ে আসবেন বলে বিদায় নিলেন। তবে একবারও ওই হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে কিছু বললেন না। যদিও ভাইয়ের জন্য প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছিল তাঁর।
মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায় সে রাতে শয্যায় গেলেন ইনভেরাওয়ি। এপাশ-ওপাশ করতে লাগলেন, কিন্তু দু’চোখের পাতা এক করতে পারছেন না। একটা বই হাতে নিলেন, যদি ওটা অশান্ত মনটাকে শান্ত করে ঘুম এনে দেয়। হঠাৎ আবিষ্কার করলেন বইয়ের পাতায় একটা ছায়া পড়েছে। বিস্মিত হয়ে ওপরপানে তাকিয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন। তাঁর বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে পালক ভাই। তবে কতকটা বদলে গেছে। মুখ ফ্যাকাসে, বসা। চুল রক্তে চুপচুপে, কপাল বেয়েও পড়ছে রক্তের ধারা। ছিন্ন কাপড়েও রক্তের দাগ।
অদ্ভুত একটা কণ্ঠে সে বলল, ‘ইনভেরাওয়ি, খুনিকে রেহাই দেবে না। রক্তের বদলে রক্ত। খুনিকে ক্ষমা করবে না…’
বিছানায় উঠে বসলেন ইনভেরাওয়ি। চোখের সামনে আনলেন হাতজোড়া। যেন দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেতে চাইছেন। আবার যখন তাকালেন ছায়ামূর্তিটা ফিকে হতে হতে অদৃশ্য হয়েছে। কেবল তার বলা কথাগুলো বাজছে জমিদারের কানে।
পরের দিনও ইনভেরাওয়ি শপথ ভাঙলেন না। প্রেতাত্মার কথা শোনার বদলে খাবার নিয়ে গেলেন মেচনিভেনের জন্য। নরকের কীটটার সঙ্গে একটা কথাও বললেন না। কেবল খাবারটা মেঝেতে ছুঁড়ে দিয়ে একবারও পিছু না ফিরে চলে এলেন।
এই রাতেও, যেমনটা তিনি আশা করেছিলেন, তাঁর পালক ভাইয়ের প্রেতাত্মা আবার হাজির হলো। হতাশা নিয়ে আবারও ওই একই সাবধানবাণী শুনলেন, ‘ইনভেরাওয়ি, ইনভেরাওয়ি! খুনিকে ক্ষমা করবে না। রক্তের বদলে রক্ত চাই।’
সকাল হতেই ইনভেরাওয়ি বুঝে গেলেন, তাঁর কর্তব্য কী। গুহায় ছুটে গেলেন। মেচনিভেনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললেন, ‘আর তোমাকে রক্ষা করতে পারব না আমি। এবার নিজের পথ দেখো।’
‘কিন্তু, স্যর,’ মিনতি করল মেচনিভেন, ‘ওরা আমাকে খুঁজে বের করে মারবে। আপনি কথা দিয়েছিলেন আমাকে বাঁচাবেন।’
‘আমি তোমাকে বাঁচাব, কথা দিয়েছিলাম,’ কাটখোট্টা গলায় বললেন, ‘কথা রেখেছিও। আর তোমাকে রক্ষা করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। খাবার নিয়ে আর এখানে আসব না আমি। হয় চলে যাও, নয় ক্ষুধায় মরো।’ বেশ স্বস্তি পেলেন সিদ্ধান্তটা নিতে পেরে। ভাইয়ের প্রেতাত্মা রাতে হানা দেবে না, আশা করলেন। রাতে ঘুমাতে গেলেন নিশ্চিন্ত হয়ে।
কিন্তু হতাশ হতে হলো তাঁকে। আগের দু’দিনের সময়েই হাজির ভূতটা। খুব ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, ‘ইনভেরাওয়ি, ইনভেরাওয়ি! একবার তোমাকে সতর্ক করেছি। দ্বিতীয়বার সতর্ক করেছি। এখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। টিকোনডেরোগাতে আবার দেখা হবে আমাদের।’ তারপরই অদৃশ্য হলো প্রেতাত্মা।
‘না, এখনও দেরি হয়নি,’ নিজেকে বললেন ইনভেরাওয়ি, ‘আমি শোধ নেব। ভাইয়ের প্রতি ভালবাসা আমার কথা দেয়ার চেয়ে বেশি কিছু। রক্তের বদলে রক্ত ঝরবে।’ ভোরের দিকে গুহার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন। মেচনিভেনকে খুন করে ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু সেখানে পৌঁছে আবিষ্কার করলেন লোকটা চলে গেছে।
ভূতটা আর হাজির হয়নি। কিন্তু তিন রাতের ওই অভিজ্ঞতা ইনভেরাওয়িকে হতাশাগ্রস্ত এক মানুষে পরিণত করল। অনেক সময়ই ক্রুচান পাহাড়ে হাঁটতে দেখা যায় তাঁকে। অনিচ্ছাকৃতভাবে ভাইয়ের সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। তাঁকে এভাবে মন্থর পায়ে উদাস দৃষ্টিতে হাঁটতে দেখে লোকেরা করুণার দৃষ্টিতে তাকায়।
‘দুঃখী জমিদার,’ বলে তারা, ‘কীভাবে এমন বদলে গেল! ভাইয়ের জন্য মনটা খারাপ থাকে সবসময় তাঁর!’ কেবল তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধবরাই জানেন সত্যি ঘটনাটা।
কিছুদিন বাদে, ১৭৫৬ সালে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায় আমেরিকায়। ৪২ রেজিমেন্টের এক মেজর ছিলেন ক্যাম্পবেল অভ ইনভেরাওয়ি। অন্য সেনাদের সঙ্গে জাহাজে চাপেন তিনি। জুনে নিউ ইয়র্ক পৌছেন তাঁরা। সেখান থেকে যান আলবেনি। ১৭৫৭ সালের বসন্ত পর্যন্ত সেখানেই মোটামুটি অলস সময় কাটে।
এক সন্ধ্যার ঘটনা। এখনও পুরানো সেই ঘটনাটাই প্রভাব বিস্তার করে আছে তাঁর ওপর। লেফটেনেণ্ট-কর্নেল গ্রান্টকে জিজ্ঞেস করলেন টিকোনডেরোগা নামের কোন জায়গার কথা শুনেছেন কিনা।
‘না,’ জবাব দিলেন কর্নেল, ‘নামটা বেশ অদ্ভুত। এর কথা জানতে চাইছ কেন? কোন গল্প আছে নাকি জায়গাটিকে নিয়ে তোমার?’
একটু দ্বিধা করলেন ইনভেরাওয়ি। ওখানে তখন অন্য অফিসাররাও উপস্থিত ছিলেন। হয়তো টিকোনডেরোগার কথা কেউ জানতেও পারেন! হয়তো এক প্রেতের সতর্ক সঙ্কেতের বিষয়টা হেসেই উড়িয়ে দেবেন। একই সঙ্গে আবার ভাবলেন কাহিনীটা তাঁর মনটা হালকা করবে। অতএব গোটা ঘটনাটাই খুলে বললেন।
কেউ কেউ বিশ্বাস করলেন তাঁর কথা। কেউ আবার এটাকে একটা গালগপ্পো বলেই ধরে নিলেন। তবে মেজরের মনের অবস্থা বুঝে কেউ তাঁকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করলেন না। অফিসারদের একজনও টিকোনডেরোগার নাম শোনেননি।
পরের বছর মেজর-জেনারেল অ্যাবারক্রমবির নেতৃত্বে লেক জর্জের ফরাসী দুর্গ সেন্ট লুইসে একটা অভিযানে যাওয়ার নির্দেশ এল। দলটি রওয়ানা হওয়ার কিছুক্ষণ আগে একজন অফিসার কর্নেল গ্রান্টকে এসে বললেন, ‘স্যর, এই মাত্র যে তথ্যটা পেয়েছি তা তোমাকে জানানো কর্তব্য মনে করছি। টিকোনডেরোগা নামটা কি মনে করতে পারছ?’
‘একটু ভাবতে দাও। টিকোনডেরোগা? কেমন পরিচিত ঠেকছে! ও, হ্যাঁ! এখানেই মেজর ক্যাম্পবেলের প্রেত ভাই ওর সঙ্গে দেখা করার কথা বলেছে। ক্যাপ্টেন হঠাৎ ওই জায়গাটির কথা বলছ কেন?’
‘কারণ, স্যর, আমরা এখন সেন্ট লুইস’ নামের যে জায়গাটিতে যাচ্ছি তা আমেরিকার আদিবাসীদের কাছে টিকোনডেরোগা নামে পরিচিত।’
‘ক্যাম্পবেলকে বিষয়টা না জানানোই ভাল,’ উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন কর্নেল, ‘যা-ই ঘটুক না কেন, তাঁর কাছে এ নিয়ে মুখ খুলবে না।’
জুলাইয়ের শুরুর দিকে রওয়ানা হয় দলটি। গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে টিকোনডেরোগার দিকে চলতে থাকে। পথে একটা যুদ্ধে ফরাসী দলকে মোটামুটি নাস্তানাবুদ করে। জুলাইয়ের দশ তারিখ শুরু হয় আসল লড়াই।
শুরু থেকেই এবার বেশ বেকায়দায় পড়ে ইংরেজ বাহিনী। কোনভাবেই ফরাসী রক্ষণ-দুর্গ ভাঙতে পারছিল না। ফরাসী গোলন্দাজ আর পদাতিকদের পাল্টা আক্রমণে রীতিমত দিশেহারা অবস্থা রেজিমেন্ট ৪২-এর।
চার ঘণ্টা ভয়াবহ যুদ্ধের পর জেনারেল অ্যাবারক্রমবি উপায়ান্তর না দেখে পিছু হটার নির্দেশ দেন। অন্তত সাতশো সেনা নিহত কিংবা আহত হয় এই লড়াইয়ে।
এঁদের মধ্যে ছিলেন ইনভেরাওয়ি। সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করলেও তাঁর ক্ষতটা এতটাই মারাত্মক যে এটা নিশ্চিত, মৃত্যু সমাগত তাঁর। পাশেই পড়ে আছে ইনভেরাওয়ির ছেলের মৃতদেহ, এই রেজিমেন্টের এক অফিসার। কর্নেল ইনভেরাওয়ির অবস্থা জানতে পারার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলেন। জমিদার চোখ পিট পিট করছেন। কথা বলার চেষ্টা করলেন। কেবল ফিসফিস করে কয়েকটা শব্দ বললেন, ‘তুমি ধোঁকা দিয়েছ…এটাই টিকোনডেরোগা… কারণ তাকে দেখেছি আমি…’ যন্ত্রণায় কালো হয়ে গেল তাঁর মুখটা। পরমুহূর্তেই মারা গেলেন।
ওই দিনের ঘটনাই, তবে অনেক দূরে স্কটল্যাণ্ডে, এডেরেইনের মিস ক্যাম্পবেল এবং তাঁর বোন কিলমালি থেকে ইনভেরারের দিকে হাঁটছিলেন। খালের ওপরের নতুন সেতুটায় এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন তাঁরা। এসময় বোনেদের একজনের আকাশের দিকে চোখ গেল। চিৎকার করে বোনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, ‘আকাশের দিকে তাকাও। জলদি। তুমিও কি দেখতে পাচ্ছ?’
ওপরে তাকাতেই মুখ হাঁ হয়ে গেল তাঁর বোনের। একটা বড় ধরনের যুদ্ধের দৃশ্য যেন মঞ্চায়িত হচ্ছে সেখানে। রং দেখে রেজিমেন্টগুলোকে আলাদা করতে পারলেন। অনেক বন্ধুকেও চিনতে পারলেন এঁদের মধ্যে। একপর্যায়ে তাঁদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে ইনভেরাওয়ি এবং তাঁর ছেলে মাটিতে পড়লেন। পরিচিত আরও অনেককেই ভূলুণ্ঠিত অবস্থায় আবিষ্কার করলেন। যখন ইনভেরারেতে পৌঁছলেন তখন খুব উত্তেজিত দু’জনেই। সব বন্ধুকে তাঁদের দেখা ওই দৃশ্যের বর্ণনা দিলেন। এমনকী কাকে কাকে পড়ে যেতে দেখেছেন, তারিখসহ লিখে রাখলেন।
শুধু তাঁরাই যে এই দৈব দৃশ্য দেখেছেন তা নয়। বেশ বিখ্যাত এক চিকিৎসক স্যর উইলিয়াম হার্ট ইনভেরারে দুর্গের পাশ দিয়ে এক বন্ধু এবং এক ভৃত্যসহ হাঁটছিলেন। তাঁরাও আকাশে ওটা দেখেন। মিস ক্যাম্পবেলদের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যায় তাঁদের অভিজ্ঞতাও।
কয়েক হপ্তা পরে টিকোনডেরোগায় এই ব্যর্থ আক্রমণের বিষয়ে একটা বিবৃতি দেয় আর্মি গেজেট। তার সঙ্গে পুরোপুরি মিলে যায় ওই দৈব দৃশ্যের বর্ণনা।
তবে গেজেট আসার বহু আগেই আরগিলে নেমে এসেছে বেদনার কালো ছায়া। জমিদার ইনভেরাওয়ির বন্ধুরা জেনে গেছেন সৎ ভাইয়ের প্রেতাত্মা তার কথা রেখেছে, ‘টিকোনডেরোগাতে আবার দেখা হবে আমাদের….
নাইটসব্রিজের ভুতুড়ে দাঁত
ঘটনাটি সংগ্রহ করেন বিখ্যাত প্রেত গবেষক ইলিয়ট ও’ডনেল।
লণ্ডনের পাতাল রেলস্টেশনের একশো গজের মধ্যে নাইটসব্রিজে একটি ফ্ল্যাট আছে। বলা হয় ওটা ভুতুড়ে। আর এর ভুতুড়ে কাণ্ড-কারখানা নিয়ে নানা ধরনের গল্প প্রচলিত আছে। এর মধ্যে একটাকে সব কিছু বিবেচনা করে সত্যের কাছাকাছি মনে হয়েছে ও’ডনেলের কাছে। এটা তিনি শোনেন বন্ধকের কারবার করা হলবোর্নের এক লোকের কাছ থেকে। এটি বরং তাঁর মুখ থেকেই শুনব আমরা।
দশ বছর আগের ঘটনা (বিশ শতকের শেষ দিকে)। মুখ ঢাকা এক নারী আমার দোকানে আসেন। বেশ কয়েকটি আংটি, একটা ঘড়ি, টাইয়ের পিন আর এক সেট নকল দাঁত, যার ওপরের পাটির দুটো খোয়া গিয়েছে আর কয়েকটা আলগা, কিনতে অনুরোধ করলেন মহিলা।
‘তোমার বিজ্ঞাপনটা পড়েছি আমি। সেখানেই ‘জেনেছি নকল দাঁত কেনো তুমি। আর এটা আমার স্বামীর, যিনি মারা গিয়েছেন। যেহেতু এটার আর কোন প্রয়োজন নেই, আমার মনে হলো বিক্রি করে দেয়াই বিবেচকের কাজ হবে। এগুলো সোনার, ঠিক না?’
‘আংশিক, ম্যাম।’ তাঁর দিকে আরও ভালভাবে দৃষ্টি দিয়ে বললাম। তাঁর কণ্ঠে এমন একটা কিছু ছিল যেটা আমার মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। মানুষের কণ্ঠ সবসময়ই আমাকে আকৃষ্ট করে। এই কণ্ঠটা খুব কর্কশ মনে হলো আমার, স্বামীর জন্য কোন আবেগের ছিটেফোঁটাও তাতে আছে বলে মনে হলো না আমার।
‘তা কত চাও তুমি?’ জানতে চাইলাম।
‘কত দেবে?’ জানতে চাইলেন ভদ্রমহিলা।
বললাম। বেশ কিছুটা দর কষাকষির পর আমার প্রস্তাবে রাজি হলেন। তারপর টাকা নিয়ে বিদায় নিলেন।
রাতে ঘুমাতে যাওয়ার সময় কেন যেন ওই মহিলার শীতল কণ্ঠস্বরটা ঘুরে-ফিরে বাজতে লাগল আমার কানে। একপর্যায়ে ঘুমিয়ে গেলাম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি, বলতে পারব না। হঠাৎ যন্ত্রণায় চিৎকার করে জেগে উঠলাম। মনে হলো নিজের একটা দাঁত গিলে ফেলেছি। মুখের ভেতর হাত দিয়ে সবগুলো দাঁতকে ঠিক জায়গায়ই পেলাম। তারপরও বারবার পরীক্ষা করতে লাগলাম। একপর্যায়ে নিশ্চিত হলাম ওটা একটা স্বপ্ন ছিল। আর গলায় দাঁত আটকে মরারও কোন সম্ভাবনা নেই আমার। সকালে ঘুম ভাঙতে গোটা ঘটনাটা মন থেকে ঝেড়ে-মুছে দূর করে দিলাম। রাতে আবারও একই ঘটনা ঘটল। একই দুঃস্বপ্ন দেখলাম। চিৎকার করে ঘুম থেকে জেগে বিছানায় উঠে বসলাম আবারও। ঘর ঘর শব্দ করছি। গলা চেপে ধরে আছি ভয়ানকভাবে। নকল দাঁতগুলোর প্রতি ভয়ানক একটা বিদ্বেষ অনুভব করলাম। যে কোন মূল্যে এর থেকে মুক্ত হতে চাইলাম। ওই সন্ধ্যায় আমার এক চিকিৎসক বন্ধুর কাছে নিয়ে গেলাম। ওটা ভালভাবে পরীক্ষা করে সে বলল, ‘পাটি থেকে ওগুলো কি টেনে তোলার জন্য জোরাজুরি করেছ?’
‘না,’ জবাব দিলাম।
‘তবে অন্য কেউ করেছে। দেখো, চিমটা বা অন্য কোন যন্ত্র দিয়ে এখানে খোঁচা মারা হয়েছে।’
যা হোক, আমার বন্ধু জিনিসটা রেখে দিল। কয়েক হপ্তা বাদে তার বাড়িতে যাওয়ার সুযোগ হলো আমার। বন্ধুটি জানাল তখন, সে রাতে ইদানীং ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখছে। তারপর হেসে জানাল আমার বেচে দেয়া দাঁতগুলোর উপস্থিতির কারণেই এটা ঘটছে বলে ধারণা তার।
‘প্রতি রাতে ঘুম থেকে জেগে উঠছি আমি। মনে হয় আমি কয়েকটা দাঁত গিলে ফেলেছি। আমার গলা দিয়ে ওগুলো নেমে যাওয়ার অনুভূতিটা এতটাই প্রকট যে বেশ কতকটা সময় লাগে ওটা যে দুঃস্বপ্ন তা বুঝতে। এই দাঁতগুলো দেয়ার আগে এ ধরনের কিছু ঘটেনি আমার জীবনে। তাই আমার মনে বিশ্বাস জন্মেছে এই সমস্যার মূলে দাঁতগুলো। এর মধ্যে আমার এক রোগীর এক পাটি সুন্দর দাঁতের প্রয়োজন হয়। খুশি মনে তার মুখে ওগুলো বসিয়ে দিয়ে এর থেকে মুক্তি পাই। পরে তাকে যখন জিজ্ঞেস করলাম তখন সে জানাল দাঁতগুলো নিয়ে বেশ আনন্দেই আছে। কোন সমস্যা হচ্ছে না।’
বিষয়টা আমাকে আরও বেশি রহস্যের মধ্যে ফেলে দিল। একদিন যে মহিলার কাছ থেকে দাঁতের পাটিটা কিনেছিলাম সে আবার আমার দোকানে এল, অন্য কিছু জিনিস বিশেষ করে পুরুষ মানুষের বিভিন্ন অলঙ্কার বিক্রির জন্য। তখন একজন কর্মচারীকে রেখে সাবধানে মহিলাকে অনুসরণ শুরু করলাম। ভাগ্য আমার সাথে ছিল। .নাইটসব্রিজের এক ফ্ল্যাটে তাকে ঢুকতে দেখলাম। সেদিনের মত চলে গেলাম। পরের কয়েকদিন নানা ব্যস্ততায় আর ওদিকে যেতে পারলাম না। তারপর একদিন হাজির হলাম। কেয়ারটেকারের কাছ থেকে জানতে পারলাম মহিলার নাম মিসেস আরবাথনট। বিধবা। অল্প কিছুদিন আগে স্বামীকে হারিয়েছেন। তার ক’দিন পর পাততাড়ি গুটিয়ে এখান থেকে চলে গিয়েছেন। তাকে কৌশলে জিজ্ঞেস করলাম মহিলার স্বামী কীভাবে মারা গিয়েছেন তা সে জানে কিনা। লোকটা জানাল দুর্ঘটনাবশত নিজের কয়েকটা নকল দাঁত গিলে ফেলেন ভদ্রলোক। তখন একটা অপারেশন করা হয় তাঁর। ওই সময়ই মারা যান। সে আরও জানাল মি. আরবাথনট মাঝে মাঝেই বেশ অসুস্থ হয়ে পড়তেন। বিশেষ করে স্নায়বিক দুর্বলতায় ভুগছিলেন। কয়েকবারই তাঁকে জলদি ডাক্তার ডেকে আনতে হয়েছে।
এখন আমার এবং দন্ত্য চিকিৎসক বন্ধুর অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে বাকি রইল না এই দাঁতের পাটির মধ্যে কোন একটা অস্বাভাবিক বিষয় আছে। আর এটা যেভাবে হোক সমাধান করতে হবে আমাকে। মিসেস আরবাথনট এবং তাঁর অতীত সম্পর্কে সেজন্য আরও জানতে হবে আমাকে। কেয়ারটেকার জানাল মিসেস আরবাথনটের মেইড র্যানির সঙ্গে দারুণ ভাব ছিল তার। তবে মিসেস পুরুষদের দেখতে পারেন না বলে এটা গোপন রাখে তারা।
কয়েকদিন পর র্যানির সঙ্গে দেখা করলাম। ঠিকানা আগেই তার প্রেমিক ওই কেয়ারটেকারটার কাছ থেকে নিয়ে রেখেছিলাম। কিছু টিপসের বিনিময়ে র্যানি আমাকে বেশ কিছু চমকপ্রদ তথ্য দিল
বলতে শুরু করল সে, ‘আরবাথনটদের পারিবারিক জীবন মোটামুটি চলে যাচ্ছিল। যদিও তাঁর স্ত্রী বয়সে অনেক ছোট ছিলেন। একজন অসুস্থ লোকের সঙ্গে ঘর করতে মহিলা খুব সন্তুষ্ট না হলেও বেশি ঝামেলাও পাকাচ্ছিলেন না। তারপরই কয়েকজন পুরুষবিদ্বেষী নারীর সঙ্গে দেখা হয়। তখন থেকেই পুরোপুরি বদলে গেলেন মিসেস আরবাথনট। স্বামীর কোন কথাই আর ভাল লাগল না তাঁর। এমনকী একটা বই কিংবা এক গ্লাস পানি এগিয়ে দিতে বললেও গালমন্দ করতেন। তাঁর ওই বান্ধবীরা যত বেশি যাতায়াত করতে লাগলেন, মিসেসও আরও বেশি উগ্র হয়ে উঠলেন।’
র্যানি আমাকে আরও জানাল একদিন মিসেস এবং তাঁর এক বান্ধবীর কথার একটা অংশ শুনে ফেলে সে। ডাইনিং রুমে ফায়ারপ্লেসের ধারে বসে ধূমপান করছিলেন এবং কথা বলছিলেন তাঁরা। তখন ডিনারের কাপড় বিছাতে যায় র্যানি। এসময় দেখে মিসেস খুব ঝুঁকে বান্ধবীর কথা শুনছেন। এসময় বান্ধবীর কিছু কথা কানে আসে তার, ‘১৮৯৬ সালের পর আর কোন মহিলার ফাঁসি হয়নি এই ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে। তাছাড়া এমন অনেকগুলো ঘটনার কথা তোমায় বলতে পারি যেখানে হার্ট অ্যাটাকে বা অন্য কোন প্রাকৃতিক কারণে মৃত্যু হয়েছে বলে ভাবা হয়েছে অথচ এর পেছনে কারও হাত ছিল। কিন্তু কেউ সন্দেহ পর্যন্ত করেনি।’ তারপর হঠাৎ গলা নামিয়ে ফেলেন মহিলা যেন নাম শুনতে না পায় র্যানি। ‘সিঁড়ির গোড়ায় ঘাড় ভাঙা অবস্থায় পাওয়া যায় তাকে। ধরে নেয়া হয় দুর্ঘটনাবশত তার মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু আমি জানি আসলে বিষয়টা তা নয়। ভদ্রলোক সবসময় মাতাল হয়ে থাকত। তাই তার স্ত্রী কোরালি ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। আমার কাছে স্বীকারও করে সে।’
র্যানি এরপর আর কিছু শোনেনি। কারণ ওই কামরা থেকে বেরিয়ে আসতে হয় ওই মুহূর্তে। তবে পরের দিন বিষয়টা কিছুটা পরিষ্কার হয় তার কাছে। ওই দিন একটু তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে পড়ে র্যানি। এসময় দেখে রান্নাঘরে তার মালকিন এক পাটি দাঁত নিয়ে কিছু একটা করছেন। তাঁর এক হাতে দুটো চিমটা, অপর হাতে দাঁতের পাটি। তারপরই তার ভেতরে ঢোকার শব্দ পেয়ে আলগোছে চিমটা আর দাঁত পকেটে ঢুকিয়ে ফেলেন। ওই দিন সকালে নাস্তার সময় র্যানি জানতে পারে মি. আরবাথনট দুই-তিনটা দাঁত গিলে ফেলেছেন। যখন ডাক্তার এলেন, মিসেস আরবাথনট তাঁকে জানালেন সবসময় স্বামীকে ঢিলা দাঁতগুলোর ব্যাপারে সতর্ক করলেও তাঁর কথায় বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করেননি তিনি। র্যানি জানাল, তবে ওই দিন সকালে কিচেনে চিমটা দিয়ে দাঁতে কী কারিগরি ফলিয়েছে এটা ‘ব্যাখ্যা করেননি একবারের জন্যও।
তবে ভদ্রলোকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরের রাতটার কথা এখনও ভুলতে পারে না র্যানি। মালকিনের অনুরোধে ওই রাতটা তাঁর বেডরুমের কাছের ড্রেসিং রুমে ছিল র্যানি। মাঝরাতে প্রচণ্ড এক চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায় তার। ঘটনাটা কী জানতে সঙ্গে সঙ্গে মিসেসের কামরায় ছুটে যায়। গিয়ে দেখে বিছানার ওপর গলা চেপে বসে আছেন মহিলা। চেহারাতে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট।
ওহ, আমি একটা দাঁত গিলে ফেলেছি। ওটা গলায় আটকে আছে আমার।’ খসখসে কণ্ঠে বললেন তিনি।
কিংকর্তব্যবিমূঢ় র্যানি বুঝতে পারছিল না কী করবে। সিঁড়ির দিকে দৌড় শুরু করেছিল; এসময় হঠাৎ মিসেস আরবাথনট শান্ত হয়ে যান।
‘এখন সব ঠিক আছে,’ হাত মুখের ভেতর থেকে বের করে বললেন, ‘একটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। তবে মনে হচ্ছিল সত্যি। তোমাকে বিরক্ত করলাম, সরি। শুভরাত্রি।’ তারপর র্যানিকে হাত ইশারায় চলে যেতে বললেন।
কিন্তু তারপর থেকে প্রতি রাতে একই স্বপ্ন দেখে চিৎকার করতে লাগলেন। র্যানি এসে দেখে, শেষমেশ বিষয়টা স্বপ্নই। এভাবে প্রতি রাতের এই ঘটনায় রীতিমত বিধ্বস্ত অবস্থা হয়ে যায় ভদ্রমহিলার। একপর্যায়ে শহর ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে গিয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন। যাবার যে সময়টা স্থির করেন এর কয়েক রাত আগে বান্ধবীদের জন্য এক ডিনার পার্টির আয়োজন করেন। সেখানেই ঘটে অদ্ভুত এক ঘটনা। র্যানি সাহায্য করছিল তার মালকিনকে। যখন মিষ্টি খাচ্ছিল সবাই তখন হঠাৎ মিসেস ডি. (যাঁর সঙ্গে মিসেস আরবাথনট শলা করেছিলেন) মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেলেন, তাঁর হাত থেকে খসে পড়ল চামচ। সবার দৃষ্টি চলে গেল তাঁর দিকে।
‘লুসি, কী হয়েছে?’ জানতে চাইলেন মিসেস আরবাথনট, ‘তুমি কি অসুস্থ? একটু ব্র্যাণ্ডি দেব?’
‘না, না!’ জবাব দিলেন মহিলা। মুখে একটা হাসি ফোটানোর চেষ্টা করলেন, ‘তেমন কিছু না। হঠাৎ আমার প্লেটে একটা দাঁত চোখে পড়ে। অবাক হয়ে ভাবলাম কোনখান থেকে এল এটা। কিন্তু এখন তো আর দেখতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে জেগে জেগেও স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি আজকাল।’
‘একটা দাঁত!’ অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠল কয়েকজন অতিথি, ‘কেন? কী অবাক কাণ্ড।’
‘কী অদ্ভুত! কোন একটা ভুল হয়েছে তোমার। হয়তো পেস্ট্রির একটা টুকরোকে দাঁত ভেবে বসে আছ। ব্র্যাণ্ডিতে কাজ না হলে ওয়াইন নিতে পার।’ মুখে কথাটা বললেও র্যানি খেয়াল করল মালকিনের চেহারাটা সাদা হয়ে গিয়েছে।
তবে রাতে যখন ঘুমাতে যান একেবারে ভোর পর্যন্ত কামরার বাতিটা নেভাননি ভদ্রমহিলা, খেয়াল করে র্যানি। আর যেদিন ফ্ল্যাট ছাড়ার কথা সেদিনই নিজের কিছু গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্তর নিয়ে বাড়ি ছাড়েন।
তবে যাবার আগে র্যানিকে সব ধরনের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে বিদায় করেন।
পরে আমি আরও খোঁজ-খবর নিই মহিলার সম্পর্কে। ওই ফ্ল্যাট ছেড়ে দিয়ে ফোকস্টোনের কাছে এক ফ্ল্যাটে ওঠেন। কিন্তু অল্প কয়দিন সেখানে থেকেই পাততাড়ি গুটিয়ে অন্য কোথাও চলে যান। আমার ধারণা যেখানেই যান বাকি জীবনটা ভয়াবহ ওই দুঃস্বপ্নের কবল থেকে রেহাই পাবেন না। আর ওই ফ্ল্যাটটা, যেখানে স্বামী-স্ত্রী থাকতেন, সেটারও সমস্যা আছে। কেউই জায়গাটায় এখন থাকতে চায় না। কেয়ারটেকার বলেছে সবাই ওই একই দাঁত গিলে ফেলার স্বপ্ন দেখে।
কুইন মেরির প্রেতাত্মারা
যখন জাহাজ ছিল তখন কুইন মেরিতে নানান ভুতুড়ে কাণ্ড- কীর্তির কথা শোনা যেত। তারপর একে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার লং বিচে বিলাসবহুল এক হোটেলে রূপান্তরিত করা হয়। আশ্চর্য ঘটনা, এরপর এতে অতিপ্রাকৃত ঘটনা কমে তো নি-ই বরং বেড়েছে। হোটেল মালিকরাও বিষয়টা ভালভাবেই নিয়েছেন। কারণ আখেরে তাঁদের লাভই হয়েছে এতে!
যেদিন প্রথম সাগরে নামে সেদিন থেকেই শুধু জাহাজকুলে নয় গোটা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে কুইন মেরির নাম। যে কোন জাহাজের উদ্বোধন বিশাল এক ব্যাপার। কুইন মেরির বেলায় আরও প্রকটভাবে কথাটা সত্যি। বিশেষ করে এর মালিকদের জন্য। ইংল্যাণ্ডের কানরাড লাইন ছিল এর মালিক। জাহাজটার পেছনে দু’হাতে টাকা খরচ করা হয়। প্রায় ১০২০ ফুট লম্বা জাহাজটির ওজন ৮১২৩৭ টন। এখানে জানিয়ে রাখা ভাল, টাইটানিক ছিল ৮৮২ ফুট লম্বা, আর ওজনে ৪৬৩২৯ টন।
১৯৩৪ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর সাগরে ভাসে কুইন মেরি। তবে এর মালিকদের হতাশ করে লেডি মেবেল ফর্টেস্কু- হ্যারিসন ভবিষ্যদ্বাণী করেন, ‘আরএমএস কুইন মেরি জনপ্রিয়তার শিখরে উঠবে তখনই যখন সে আর সাগরে নামবে না এমনকী কোন যাত্রীও বহন করবে না। তার এই সাফল্য দেখে যাওয়ার জন্য এখনকার অনেকেই থাকবে না, এমনকী আমিও।’
সত্যি তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী যখন সত্যি হলো তখন তা দেখবার জন্য বেঁচে নেই ফর্টেস্কু-হ্যারিসন। ব্রিটিশ জাহাজ, যেটা কিনা একসময় পরিচিত ছিল ‘আটলান্টিকের রানি’ হিসাবে, সেটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে একটি ভাসমান হোটেল হিসাবে। ১৯৯০-এর দশকে কুইন মেরি হোটেলের পাবলিক রিলেশন অফিসার হিসাবে কাজ করা এলিজাবেথ বোর্সটিঙের মতে ফি বছর হাজার হাজার অতিথি ভাসমান হোটেলটিতে আসে শুধু এখানকার অশরীরীদের কাণ্ড-কীর্তি দেখার জন্য।
হোটেলে পরিণত হবার পর যেন ভুতুড়ে হিসাবে এর সুখ্যাতি কিংবা কুখ্যাতি আরও বহুগুণ বেড়ে যায়। ওখানে অন্তত গোটা বিশেক অতৃপ্ত প্রেতাত্মাকে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। ধারণা করা হয় এদের সবগুলোই জাহাজ হিসাবে সাগরে ঘুরে বেড়াবার সময় থেকেই এর সঙ্গী। তবে তখন এদের প্রতাপটা আরও কম ছিল।
প্রথম ছয় বছরের ভ্রমণে জাঁকালো জাহাজটি রাজকীয় অতিথি, নায়ক-নায়িকাসহ ধনকুবেরদের খুব পছন্দের ছিল। তারপরই ১৯৩৯ সালের ৩০ আগস্ট বদলে যায় সব কিছু। সেবারের বিলাসযাত্রায় জাহাজে ছিলেন ২৫৫০ জন ধনী ও নামী-দামি ব্যক্তি। সেই সঙ্গে প্রায় সাড়ে চার কোটি ডলারের স্বর্ণপিণ্ড বহন করছিল কুইন মেরি। হঠাৎই নির্দেশ এল জাহাজের ২০০০-এর বেশি ঘুলঘুলির সবগুলো ঢেকে দেয়ার জন্য। গোটা জাহাজের সব যাত্রীর জীবন নির্ভর করতে থাকে তখন কারও চোখে ধরা না পড়ার ওপর। কারণ ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স কেবলই জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আটলাণ্টিকের বরফশীতল জল ঢেকে গেছে নাৎসী যুদ্ধ জাহাজ ও সাবমেরিনে।• আকাশে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে হিটলারের অনুগত বাহিনীর যুদ্ধবিমান।
সৌভাগ্যক্রমে যাত্রার বাকি সময়টা জার্মানদের নজরে পড়ল না কুইন মেরি। এটাই ছিল প্রমোদতরী হিসাবে এর শেষ ভ্রমণ। তারপর একে রূপান্তরিত করা হয় সেনাবাহী এক জাহাজে, যেটার ডাক নাম ছিল, ‘গ্রে গোস্ট’ বা ‘ধূসর প্রেতাত্মা’। বন্দরে পৌছার সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের ভেতর থেকে আরাম-আয়েশের সব উপাদান ঝেঁটিয়ে বিদায় করা হয়। জাহাজটির বাইরের অংশ মেটে ধূসর রং করা হয়। শত্রুর চোখের আড়ালে রাখার জন্যই এটা করা হয়।
যুদ্ধকালীন সময়ে আটলান্টিক পাড়ি দেয়া ছিল খুব ঝুঁকিপূর্ণ। জাহাজটির ২৮.৫ নট গতিকে কাজে লাগানোর জন্যই এর এই রূপান্তর। যদিও এর দুরন্ত গতিই যুদ্ধের সময়ের ভয়াবহ এক দুর্ঘটনার মূল কারণ। বলা হয় কুইন মেরির গায়ে ভুতুড়ে তকমা লাগার প্রধান কারণও এটি। কুইন মেরি ও তার অনেক ছোট পাহারাদার সঙ্গী কারাকোয়া একসঙ্গে ভ্রমণ করছিল। জার্মানদের বোকা বানানোর জন্য এলোমেলো বা আরও পরিষ্কারভাবে বললে আঁকাবাঁকাভাবে চলছিল জাহাজদুটি। কোনভাবে হিসাবে একটা ভুল হয়ে যায়। ‘ধূসর প্রেতাত্মা’ সরাসরি গিয়ে আঘাত করে কারাকোয়াকে। প্রচণ্ড গতির বিশাল দানবাকৃতি জাহাজের ধাক্কায় আক্ষরিক অর্থে দুই টুকরো হয়ে যায় কারাকোয়া।
প্রহরী জাহাজের ৪৩৯ জন নাবিকের ৩৩৮ জনই মারা যায়। এদের বেশিরভাগেরই মৃত্যু হয় আটলান্টিকের হিমশীতল জলে ডুবে। তাদের চোখের সামনেই বড় জাহাজটি ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছিল, কারণ যুদ্ধকালীন সময়ে থেমে মৃত্যুপথযাত্রী লোকগুলোকে উদ্ধারে কঠোর নিষেধাজ্ঞা ছিল। একই সঙ্গে দুর্ঘটনা এবং ডুবন্ত লোকগুলোকে ফেলে পালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ-এতটাই মানসিকভাবে বিধ্বস্ত করে ‘ধূসর প্রেতাত্মা’-র নৌসেনাদের যে ওই জাহাজের পরিবেশটাই অন্যরকম হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে তখন থেকেই অতিপ্রাকৃত কিছুর আছর হয় এর ওপর।
নিরাপদে বন্দরে ভেড়ার সঙ্গে সঙ্গে ৭০ টন সিমেন্ট দিয়ে মেরামত করা হয় জাহাজটি। কিন্তু এটা মোটেই নাবিকদের মনোজগতে কিংবা এর ওপর যে অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রকাশ ঘটেছে তাতে কোন প্রলেপ দিতে ব্যর্থ হলো। এত কিছুর পরও যুদ্ধে দারুণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে গেল জাহাজটি। এমনকী যুদ্ধের চূড়ান্ত মুহূর্তে ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন চার্চিল সবসময় আটলান্টিক পাড়ি দিতে কুইন মেরিকে বেছে নিতেন।
১৯৪৫ সালে শান্তি ফিরে এলেও প্রমোদতরী থেকে নৌসেনা আনা-নেয়ার যানে রূপান্তরিত জাহাজটি সেনা, নাবিক ও বৈমানিকদের সেবাতেই ব্যবহৃত হতে লাগল। বলা চলে আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে সে এখন। মোট ১৩০০০ যুদ্ধবিধবা এবং তাদের সন্তানদের আমেরিকা এবং কানাডায় পৌঁছে দিল। এজন্য মোট ছয়বার ভ্রমণ করতে হয় একে। পরের বিশ বছর কুইন মেরি আবারও যাত্রী পরিবহন করল। এর মধ্যে মাঝে মাঝে ছিলেন সমাজের অভিজাত ব্যক্তিরাও।
১৯৬৭-র ডিসেম্বরে কুইন মেরির সাগরযাত্রার অবসান ঘটল। অবসরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হলো তাকে। এসময় একে কিনে নিল আমেরিকার শহর লং বিচ কর্তৃপক্ষ। সাড়ে ৩৪ লাখ ডলার দিয়ে জাহাজটি কিনল তারা। স্থায়ীভাবে তার জায়গা হলো লং বিচে। এর মাধ্যমে একত্রিশ বছর আগে লেডি মেবেল ফর্টেস্কু-হ্যারিসনের করা ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হবার পথে প্রথম ধাপ সম্পন্ন হলো। এরপর থেকে জাহাজটি আর কোন যাত্রী বহন করেনি। তেমনি আর একবারের জন্যও সাগরে যাত্রা করেনি। এদিকে ব্রিটিশ জাহাজের তালিকা থেকে বাদ দেয়া হলো জাহাজটির নাম। একটি দালান হিসাবে একে নথিভুক্ত করা হলো। এর জনপ্রিয়তাকে পর্যটক টানার কৌশল হিসাবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিলেন মালিকেরা। জাহাজটিকে হোটেলে রূপান্তরের কার্যক্রম শুরু হলো।
এসময়ই মালিকরা আবিষ্কার করলেন এর ব্যতিক্রমী অতীতের কারণে এখানে আস্তানা গেড়েছে বহু প্রেতাত্মা। হালের যে অংশটা কারাকোয়াকে আঘাত করে ওই অংশটিতে ভুতুড়ে কাণ্ড-কীর্তির সংখ্যা যেন বেশি। একজন কর্মচারী ওই জায়গাটিতে রাতে একটা রেকর্ডার রেখে যায়। পরদিন রেকর্ড অন করতেই দুটো জাহাজ ঠোকাঠুকির ভয়ানক আওয়াজ শোনা গেল। কেউ কেউ আবার এই জায়গায় নানা ধরনের অদৃশ্য কণ্ঠ ও রক্ত হিম করা চিৎকার শুনতে পাওয়ার দাবি করে।
অনেকেই অদ্ভুত সব আওয়াজ শোনার কথা বলে। কেউ বলে জাহাজের গায়ে হাত দিয়ে ঠক ঠক করার শব্দ শুনতে পেয়েছে। কেউ আবার প্রমত্ত ঢেউয়ের এবং ধাতব পদার্থ ছেঁড়ার আওয়াজ শোনে। তবে সবচেয়ে ভয়াবহ হলো অশুভ চিৎকার এবং গোঙানি। লোকে বলে ওই প্রহরী জাহাজের ক্রুদের চিৎকার ওগুলো। মৃত ওই নাবিকেরা কোনভাবে কুইন মেরির পরিবেশের সঙ্গে আটকে গিয়েছে।
অবশ্য এসব ঘটনার শুরু কিন্তু কুইন মেরি হোটেলে পরিবর্তিত হওয়ার আগে থেকেই। কুইন মেরির একসময়কার চীফ ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন জন স্মিথ। অবসর নেয়ার পর ওই সংঘর্ষে জাহাজের যে অংশটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেখানে কোন কিছু দিয়ে আঘাত করার ও ঢেউ বাড়ি খাওয়ার ছলাত ছলাত শব্দ শুনতে পাওয়ার কথা বলেন। জাহাজটাকে খুব ভালভাবে চিনতেন স্মিথ। শব্দের উৎস খুঁজে বের করার জন্য চিরুনি অভিযান চালালেন। কিন্তু এসব শব্দের কোন ব্যাখ্যা আবিষ্কারে ব্যর্থ হন। শেষ পর্যন্ত উপসংহারে পৌঁছেন বহু বছর আগের ওই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পৈশাচিক প্ৰতিধ্বনি শুনতে পেয়েছেন।
যুদ্ধকালীন সময়ের সেই দুর্ঘটনার পাশাপাশি তৈরির সময় এক বিস্ফোরণেও কিছু প্রাণহানি হয় জাহাজটিতে। এগুলোতে নিঃসন্দেহে এর ভেতরে অতিপ্রাকৃত শক্তি জেঁকে বসে। তারপর আবার জাহাজে অন্তত ৪৮টি অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে।
এদেরই একজন জন পেডার। ডেকের নিচে ডোরওয়ে ১৩ এই তরুণ ক্রুর জন্য প্রচণ্ড অশুভ হয়ে দেখা দেয়। ১৯৬৬ সালের ১০ জুলাই ১৮ বছরের এই তরুণ তার রুটিন কাজ করছিল। হঠাৎ ওয়াটার টাইট দরজা বন্ধ হয়ে মৃত্যু হয় তার। এলিজাবেথ বোর্সটিং স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন, নীল ওভারঅল পড়া শ্মশ্রুমণ্ডিত এই তরুণের অবয়বকে পুরানো ইঞ্জিন রুমের আশপাশে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে প্রায়ই।
এখনকার কর্মচারীরা ছাড়াও পর্যটকদের অনেকেরও আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়েছে। একসময় কুইন মেরি হোটেলের ট্যুর গাইড এবং সিকিউরিটি অফিসার ছিলেন ন্যান্সি ওজনি। বলেন, এক রাতে পর্যটনের এলাকাটা বন্ধ করার সময় পাশে কিছু একটার উপস্থিতি টের পান, ‘ঘুরে দেখলাম একজন লোক আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।’ অবশ্য তিনি স্বীকার করেছেন একজন পর্যটকের পেছনে রয়ে যাওয়া অসম্ভব কিছু না। তবে লোকটার যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে অন্য কিছু মনে হতেই পারে আপনার। ওই রহস্যময় লোকটির পরনে ছিল ময়লা নীল ওভারঅল, মুখে দাড়ি, গায়ের রং অস্বাভাবিক রকম সাদা, চেহারাটা আশ্চর্য ভাবলেশহীন। সব কিছু মিলিয়ে তাকে কোনভাবেই পর্যটক মনে হচ্ছিল না।
জাহাজের ভেতরের সুইমিং পুলটা এখনও আছে। তবে কেবলমাত্র মানুষের দেখার জন্যই এটা। এখন আর রক্তমাংসের কোন সাঁতারু ব্যবহার করে না। তবে দু’জন নারী ভূতকে এর সুবিধা নিতে দেখা যায়। একজন ট্যুর গাইডের অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা হয়। তার মনে হয় অন্য পৃথিবীর কিছু একটা দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। সাঁতারুর পোশাক পরে ছিল ওই প্রেতাত্মাটা। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে রহস্যময় সেই সাঁতারু যেমন হঠাৎ হাজির হয় তেমনি হঠাৎ গায়েব হয়ে যায়।
আরেকজন গাইড জানায় এক নারীকে ১৯৩০-এর দশকের একটা সাঁতারের পোশাক পরে একটা প্রায় শুকনো সুইমিং পুলে লাফ দেয়ার প্রস্তুতি নিতে দেখে। ওই মহিলাকে লাফ না দিতে সতর্ক করে চিৎকার দিয়ে ওঠে গাইড। তারপর সিকিউরিটি গার্ডের খোঁজে তাকায়। যখনই আপাতদৃষ্টিতে আত্মহত্যা করতে যাওয়া মহিলার দিকে ফেরে, দেখে সে সেখানে নেই।
১৯৮৩ সালের ঘটনা। কুইন মেরি হোটেলের কর্মচারী লেস্টার হার্ট সুইমিং পুলের এক পাশে ছিল। এসময় উল্টো পাশে সোনালী চুলের, ফুল হাতা সাদা গাউন পরা এক নারীকে দেখতে পায়। কিন্তু নারীমূর্তিটাকে খুব ঝাপসা মনে হচ্ছিল তার। যেন মাঝখানে একটা স্বচ্ছ পর্দা আছে। তারপর আরও ঝাপসা হতে হতে মিলিয়ে যায় ওটা।
এতে বেশ হকচকিয়ে গেলেও এ ধরনের ঘটনার জন্য কিছুটা হলেও মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যায়। একদিন সুইমিং পুলের কাছেই পর্যটকদের জন্য বানানো একটা দোকানে কাজ করছিল সে। এসময় পানির ঝপাৎ ঝপাৎ শব্দ শুনতে পায়। যেন কেউ সাঁতার কাটছে। সুইমিং পুলে সামান্য হলেও পানি রাখা হত দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য। তাই হার্টের মনে হলো কোন অতিথি হয়তো সীমা অতিক্রম করে এতে গোসল করতে নেমে পড়েছে। যে কাজ করছিল তা বাদ দিয়ে সুইমিং পুলের দিকে দৌড়ল সে। ওখানে কেউ নেই। তবে নিচে নামার মইয়ের কাছের পানি তখনও কাঁপছে। ভেজা এক পায়ের ছাপ এগিয়ে গিয়েছে ডেক ধরে এক দরজার দিকে।
ওটা দেখে হার্টের মনে হয় কোন একজন বেপরোয়া অতিথির কাণ্ডই এটা। অতএব পায়ের ছাপ অনুসরণ করা শুরু করে। মনে আশা এটা তাকে সাঁতারুর কাছে নিয়ে যাবে। তারপরই হঠাৎ করে অদৃশ্য হলো পায়ের ছাপ। সবচেয়ে আশ্চর্য ঘটনা, এখানকার খুব স্পর্শকাতর অ্যালার্ম সিস্টেম সর্বক্ষণ চালু থাকলেও পুলের চৌহদ্দিতে কোন কিছুর উপস্থিতি ওটা শনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে।
হার্ট নিশ্চিত হয়ে গেল সুইমিং পুলের কোন একটা প্রেতাত্মার উপস্থিতিই একটু আগে টের পেয়েছে। হয়তো ১৯৩০-এর দশকের সুইমিং স্যুট পরা প্রেতাত্মাটাই এটি। এদিকটাতেই আরেকটা প্রেতাত্মার আনাগোনার কথা বলে অনেকে। ওটার পরনে থাকে ১৯৬০-এর দশকের পোশাক।
আরও কিছু প্রেতাত্মার আড্ডাখানা এই সুইমিং পুল এলাকা। সাধারণত একটা শিশু কণ্ঠের হাসি শোনা যায়। তবে কখনও একটা গোমড়ামুখো ছোট্ট বালকের অবয়বও চোখে পড়ে। হয়তো সে এতটা অসুখী থাকত না যদি জানত তার মত আরও অনেক অতৃপ্ত আত্মার আবাসস্থল এই কুইন মেরি জাহাজ বা হোটেল। কুইন মেরির একটা কামরা আগে শিশুদের খেলার জায়গা হিসাবে ব্যবহৃত হত। এখন ওটা স্টোর। ওখানে অনেকেই শিশুদের খেলার শব্দ শুনতে পায়, যদিও কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না। জন্মের অল্প পরে মৃত্যুবরণ করা একটা বাচ্চার কান্নাও শোনা যায় কখনও কখনও।
তবে এই হোটেলের সবচেয়ে বিখ্যাত ভূত নিঃসন্দেহে উইন্সটন চার্চিল। যদিও তাঁর প্রেতাত্মাকে নিয়মিত দেখা যায় না। স্টোররুমে এখনও হঠাৎ হঠাৎ তাঁর বিখ্যাত সিগারের ধোঁয়া ভেসে বেড়াতে দেখা যায়। কখনও ওটার গন্ধও পান কেউ কেউ।
কুইন মেরি জাহাজের ভাণ্ডার . রক্ষক, যে এক ডাকাতিচেষ্টার সময় মারা যায়, সে-ই নাকি বি-৩৪0 কামরাটাকে ভুতুড়ে করে রেখেছে। হোটেলের অনেক অতিথিই বিভিন্ন বস্তু যেমন কাপ-প্লেট কামরাটায় উড়ে বেড়াতে দেখেছেন, কখনও আপনাআপনি খোলে, বন্ধ হয় ড্রয়ারগুলো। আবার ঘুমাতে গেলে তাদের বিছানা ধরে কেউ টানতে থাকে।
আরও কয়েকটি প্রথম শ্রেণীর কামরাও অতিপ্রাকৃত উপস্থিতির জন্য বিখ্যাত। রাতে শোনা যায় পানি পড়ার শব্দ। সকালবেলা বিনা কারণে বেজে ওঠে ফোন। মাঝরাতে হঠাৎ একে একে জ্বলতে শুরু করে একটার পর একটা বাতি। অতিথিরা শুনতে পান ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ, কখনও আবার অদৃশ্য কোন শক্তি টান দিয়ে নিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে তাদের কম্বল।
জাহাজের রান্নাঘরটা যেখানে ছিল সেখানে একটা অতিপ্রাকৃত কিছুর আনাগোনা আছে। ধারণা করা হয় সেটি খুন হওয়া এক ব্যক্তির আত্মা। প্রচণ্ড রাগী ও অশান্ত এক আত্মা ওটা। এমনকী যখন ‘গ্রে গোস্ট’ নাম নিয়ে যুদ্ধকালীন সময়ে ঘুরে বেড়াত তখনও এর উপস্থিতির কথা শোনা যায়। ওই সময় সামরিক বাহিনীতে যোগ দেয়া এক তরুণ রাঁধুনিকে আক্রমণ করে। ওই ঘটনা নিয়ে জাহাজে অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে এবং একপর্যায়ে ওই তরুণকে একটা গরম স্টোভের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলা হয়। কিচেনের চারপাশে এখনও প্লেট, কাপ এসব ছুঁড়ে মারে ওই অতৃপ্ত আত্মা। কখনও অবিচারের শিকার হওয়া লোকটার করুণ আর্তনাদ শোনা যায়। ওই জায়গার বাতিগুলো আপনাআপনি জ্বলতে নিভতে থাকে। রান্নাঘরের নানা সরঞ্জাম গায়েব হয়ে যায় হঠাৎ হঠাৎ।
কুইন মেরির সব ভূতেরাই যে মানুষ ছিল তা নয়। একটা কুকুরের চিৎকার শোনা যায় প্রায়ই। জীবিত থাকা অবস্থায় ওটা ছিল একটা আইরিশ সেটার। বলা হয় মালিকের খোঁজে সবসময় ছটফট করতে থাকে ওই কুকুরভূত। কুইন মেরি যখন একটা প্রমোদতরী ছিল তখন পোষা প্রাণী জাহাজে তোলা যেত। তবে ভিআইপি যাত্রী ছাড়া অন্যদের পোষা প্রাণীদের রাখতে হত সানডেকের একটা বিশেষ কামরায়। ওটাই খোঁয়াড় হিসাবে ব্যবহৃত হত। এক ইংরেজ যখন ভ্রমণে বের হতেন সঙ্গে নিয়ে যেতেন প্রিয় আইরিশ সেটার কুকুরটাকে। ভাল প্রশিক্ষণ পাওয়া কুকুরটা মালিকের সঙ্গে জাহাজের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে খুব ভালবাসত। তবে সে এটাও জানত এরপর তাকে আবার আটকা পড়তে হবে ওই খোঁয়াড়ে।
তো এই রুটিনটা নিত্যই চলে আসছিল। একদিন হঠাৎ কুকুরটা জোরে জোরে চেঁচাতে লাগল এবং কুকুর রাখার ঘরটার দরজায় জোরে জোরে আঁচড়াতে লাগল। মনে হচ্ছে যেন ওখান থেকে বেরিয়ে যেতে চায় সে। আপাতদৃষ্টিতে ওটার মধ্যে কোন সমস্যা দেখা যাচ্ছিল না। কিন্তু অস্থিরভাবে গোটা কামরাটা চক্কর কাটতে শুরু করে।
খোঁয়াড়ের সুপারভাইজার একজনকে পাঠাল কুকুরের মালিকের কেবিনে। আশা করল হয়তো মালিক তার প্রাণীটাকে শান্ত করতে পারবেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখা গেল লোকটা বিছানায় মরে পড়ে আছে। কুকুরটা নিশ্চয়ই অজানা কোনভাবে নিজের বন্ধু ও প্রভুর মৃত্যু টের পেয়েছিল। তাই এমন অস্থির আচরণ করছিল।
কুকুরটা এতটাই আঘাত পায় ঘটনার অল্প কিছুদিনের মধ্যে সে-ও মারা যায়। এখনও তার আর্তনাদ শোনা যায়। কেউ কেউ ওই শব্দ অনুসরণ করে এর উৎস খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু যতই সেদিকে যেতে থাকে ভুতুড়ে আওয়াজটা আরও দূরে সরে পড়তে থাকে। হয়তো এটা দিয়ে বোঝা যায় দুর্ভাগা প্রাণীটা এখন মানুষের ধরাছোঁয়ার চেয়ে অনেক দূরে।
সিনিয়র সেকেণ্ড অফিসার উইলিয়াম স্টার্কের প্রেতাত্মাকে শনাক্ত করা যায় খুব সহজেই। কারণ বিশাল কুইন মেরির গোটা এলাকাজুড়ে চক্কর দিতে দেখা যায় তাকে। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বরে জাহাজেই মৃত্যু হয় স্টার্কের। মাতাল অবস্থায় ভুলে বোতল থেকে টেট্রাক্লোরাইড খেয়ে ফেলে সে। সাথে সাথে মৃত্যু হয় তার। শেষ ককটেলটা যে ভয়ানক বিষাক্ত ছিল এখনও এ ব্যাপারটা বুঝতে না পারায় তার অতৃপ্ত আত্মাটা দ্বিধাগ্রস্তভাবে ঘুরে বেড়ায় হয়তো। তবে একেবারেই নিরীহ ধরনের আত্মা সে।
সাদা ইউনিফর্ম পরা এবং অনেকগুলো সম্মানসূচক ফিতা জামায় আটকানো আরেক গর্বিত নাবিকের আত্মাকেও ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় কুইন মেরিতে। প্রত্যক্ষদর্শীরা বলে তার অবয়বটা পরিষ্কার হলেও একেবারে স্বচ্ছ।
কুইন মেরির প্রধান লাউঞ্জ এখন কুইন’স সেলন বা অভ্যর্থনা কক্ষ হিসাবে পরিচিত। এখানেও আছে এক অশরীরীর আনাগোনা। কর্মচারীদের বর্ণনায় সাধারণ এক সাদা সান্ধ্য পোশাকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় অপরূপা এক নারীকে। কখনও ছায়ার মধ্যে একাকী নাচে সে। হোটেলে ভ্রমণের সময় একটা ছোট্ট মেয়ে এমন একজনের কথা বলে। গাইড কিছু না দেখতে পেয়ে ট্যুর চালিয়ে যায়। মেয়েটা বারবার ওই নারীকে দেখার কথা বলতে থাকে। অবশ্য মেয়েটার মত আরও অনেক পর্যটকই তাকে দেখেছে।
কুইন মেরির একটা অংশকে পুরানো এক ইংলিশ পানশালার আদলে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এখানে একটা অশরীরীর উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। সবসময় নিজের উপস্থিতি জানান দেয় না সে, যখন দেয় রীতিমত জাহির করে। একটার পর একটা প্লেট উড়ে গিয়ে আছড়ে পড়তে থাকে দেয়ালে। ঝুলতে থাকা ছবি এমনকী ঘড়িও উল্টো হয়ে যায়।
ইঞ্জিন রুম যেখানে ছিল সেখানে সাদা ওভারঅল পরা একটা লোককে কাজ করতে দেখা যায় কখনও। ধারণা করা হয় জাহাজের গোড়ার দিকের এক অফিসার তিনি। মেইন ডেকের নিচে আরেকটা অতিপ্রাকৃত শক্তির উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। যদিও দেখা যায় না তাকে। তার দৌড়ে যাওয়ার এবং ওই সময় শিকল নাড়ানোর শব্দ পাওয়া যায়।
যেখানে প্রথম শ্রেণীর স্যুইটগুলো সেখানে চমৎকার পোশাকের ফিটফাট এক আত্মাকে দেখা যায়। কালো চুলের লোকটার গায়ে থাকে ১৯৩০-এর দশকের একটি স্যুট। এক আলোকচিত্রী নিজের অজান্তেই তার ছবি তুলে ফেলে। ওই ট্যুর গাইড জাহাজের ভেতরের ছবি নিচ্ছিল। এক পর্যায়ে একটা আয়নার ছবি তোলে সে। যখন ছবিগুলো ধোয়া হয় আয়নায় লম্বা, কালো চুলের এক লোকের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। বিষয়টা অস্বাভাবিক মনে হওয়ার কারণ ছিল না, কিন্তু সমস্যা হলো লোকটার পরনের স্যুটটা ছিল ১৯৩০-এর দশকের। যে সময় ছবি তোলা হয় তখন ট্যুর গাইড একাই ছিল। আর সে নিশ্চয়ই এত পুরানো জমানার একটি স্যুট পরে ছিল না।
কেউ জানে না কুইন মেরির কয়টা ভূত বাতি জ্বালা- নেভানোর খেলায় অংশ নেয়। তেমনি বন্ধ দরজা খুলে যাওয়া কিংবা খোলা দরজা বন্ধ হয়ে যাওয়া অতি স্বাভাবিক ঘটনা। এখানকার একটা ভূত এসব বিষয়ে অবিশ্বাসী রিপোর্টার টম হেনিসির ধারণা বদলে দেয়।
১৯৮৩ সালের মার্চের একটা রাত কুইন মেরিতে একা কাটান টম হেনিসি। এই রাতটির কথা ভুলবেন না কখনও। পরিকল্পনামত কুইন মেরির সবচেয়ে ভুতুড়ে জায়গাগুলোয় রেখে যাওয়া হয় তাঁকে। শ্যাফট অ্যালিতে কাটান পঁয়ত্রিশ মিনিট। এসময় অস্বাভাবিক একটা কিছু তাঁর সঙ্গে যোগ দেয়। হঠাৎ ভুতুড়ে একটা দুম দুম শব্দ কানে আসে। সাহসের সঙ্গে শব্দ লক্ষ্য করে এগোন তিনি। কিন্তু যখনই কাছে আসেন ওটা থেমে যায়। ঘুরে যেদিক থেকে এসেছেন সেদিকে রওয়ানা দেন। এসময়ই তাঁর পথে কোথা থেকে এসে পড়ে বিশাল এক তেলের ড্রাম। ঘুরে অপর একটা পথ বেছে নেন। তারপর কী মনে করে আবার পুরানো পথে ফিরে আসেন। এবার পথ আটকাল একটা নয় বরং দুটো তেলের ড্রাম। এসময়ই মনে হলো তাঁর পায়ের নিচের ক্যাটওয়াক কাঁপছে। যেন কিছু একটা তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। হেনিসি এবার আর সাহস ধরে রাখতে পারলেন না। ঘুরে অন্য দিকে ছুটলেন।
মোটামুটি স্নায়ু শান্ত হয়ে এসেছে তাঁর। এসময় মনে হলো কাছেই কোথাও কয়েকজন মানুষ কথা বলছে। কান পাততেই বুঝলেন তিনজন লোক আলোচনায় মগ্ন। একপর্যায়ে কেবল একজনের কথা শুনতে পেলেন। তবে ওই একজনের কথাটা পরিষ্কার শুনতে পেলেন। সে বলছে, ‘বাতিটা নিভিয়ে দিচ্ছি আমি।’ সৌভাগ্যক্রমে অন্ধকারে নিমজ্জিত হবার আগেই আতঙ্কিত রিপোর্টার শ্যাফট অ্যালি থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন।
টম হেনিসি কুইন মেরি থেকে বেরিয়ে এলেন এক বদলে যাওয়া মানুষ হিসাবে। ওই জায়গায় আর কখনও একা সময় কাটানোর কথা চিন্তাই করেননি তিনি। হাজারো মানুষ ফি বছর কুইন মেরি হোটেলে ভ্রমণ করে নিদেন পক্ষে একটা ভূতকে দেখার জন্য। অনেকের ইচ্ছা পূরণও হয়।
শেষ কথা, ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি হলিউডে মৃত্যুবরণ করা লেডি মেবেল ফর্টেস্কু-হ্যারিসনের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। কুইন মেরি স্থায়ীভাবে ডকে জায়গা নেয়ার পরেই খ্যাতির চূড়ায় উঠল। যখন ভবিষ্যদ্বাণী করেন তখন ওটা অবিশ্বাস্যই মনে হয়েছিল, কিন্তু ওটার উদ্বোধনের সময় তাঁর বলা কথাগুলো অতীতের জাহাজ, অধুনা এই জনপ্রিয় হোটেলের সঙ্গে তাঁর নামটাও ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় করে রাখল।
আইরিশ কনের ভূত
ছেলেটা যদি চিৎকার করে না উঠত, তবে বেবিসিটার মেে ভেবে বসত সে স্বপ্ন দেখছে।
পুরনো কিনসেল দুর্গ এবং এর ভূতের গল্পটা মেয়েটার জানা। এখানে বদলি হয়ে নতুন আসা অফিসার এবং তাঁর পরিবারের বাচ্চাদের দেখাশোনার দায়িত্ব নিতে রাজি হওয়ায় এমনকী বন্ধুরা তাকে গালমন্দও করেছিল। কিন্তু সাগরতীরের আইরিশ এই বন্দরশহরে একটা তরুণী মেয়ের জন্য পছন্দসই চাকরি জোগাড় করা মোটেই সহজ ছিল না। তাছাড়া এসব ভূত-প্রেতের কিচ্ছায় তার বিশ্বাস নেই। তারপরই শ্বেতবসনা ওই নারীকে সে নিজেই দেখে বসল।
কয়েক ঘণ্টা আগেই বাচ্চাদুটো ঘুমিয়ে পড়েছে। তবে তরুণী জেগে ছিল। ছোট্ট ছেলে আর মেয়েটার সঙ্গে একই কামরায় ঘুমাতে একটুও খারাপ লাগে না তার। এটা তার চাকরির অংশ। সে বাচ্চাদের পছন্দ করে এ ব্যাপারেও সন্দেহ নেই। ঘুমন্ত অবস্থায় তাদের নিয়মিত কোমল শ্বাস- প্রশ্বাসের শব্দ তাকে আনন্দ দেয়। ছোট্ট বিছানাদুটোর দিকে তাকিয়ে হাসল মেয়েটা। এসময়ই কামরাটার অপর পাশে একটা কিছুর দিকে দৃষ্টি গেল তার।
তরুণী এক নারীর দেহ এগুচ্ছে বাচ্চাদুটোর দিকে। গোটা পোশাকটা সাদা। দেখে পুরানো দিনের বিয়ের পোশাকের কথা মনে পড়ে। কাপড়ের সাদা ফুলের মত সাদা তার মুখ ও হাত। কামরাটার ওই পাশে কোন দরজা কিংবা জানালা নেই। তাহলে সে এল কোন্ দিক থেকে? আবার মেঝের ওপর দিয়ে আসছে যে কোন শব্দই হচ্ছে না। মনে হচ্ছে ভেসে ভেসে এগুচ্ছে।
মেয়েটা এতটাই ভয় পেয়ে গিয়েছে যে, নড়তে পর্যন্ত পারছে না। দু’জনের মধ্যে ছোট যে বাচ্চাটা, ভেসে ভেসে তার কাছে গিয়ে থেমে গেল শ্বেতবসনা নারী। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে শুধু চেয়েই আছে ন্যানি মেয়েটা। ছোট্ট ছেলেটির হাতজোড়া বুকের ওপর ভাঁজ করা। দীর্ঘক্ষণ ঘুমন্ত শিশুটির দিকে তাকিয়ে থাকল নারীমূর্তিটি। তারপর ফ্যাকাসে একটা হাত আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে ছেলেটার কবজি স্পর্শ করল।
‘তোমার ঠাণ্ডা হাতটা সরাও।’ চেঁচিয়ে উঠল ছেলেটা। তবে সে পুরোপুরি জেগে ওঠার আগেই বাতাসে মিলিয়ে গেল শ্বেতবসনা নারী।
‘এটা সত্যি, স্যর, আমি নিজ চোখে দেখেছি! এখন যেমন তখনও তেমনি পূর্ণ সজাগ ছিলাম। আমার মনে হয় না ছেলেটাকে আঘাত করার কোন ইচ্ছা তার ছিল। তবে ও মহিলার স্পর্শ টের পায়। বড্ড শীতল ছিল ওটা। তাই ঘুমের মধ্যেই চেঁচিয়ে ওঠে।’
তরুণ কর্মকর্তাটি মাথা নাড়লেন। হয়তো, কিনসেল দুর্গের শ্বেতবসনা নারীর কাহিনী সত্যি! তাঁর আগে এখানে বদলি হয়ে আসা অনেক অফিসারই ওই নারী কিংবা তার প্রেতাত্মাকে দেখার দাবি করেছেন। সবার বর্ণনাও ছিল একই রকম। ফ্যাকাসে চেহারার এক নারী, পুরানো ধরনের কনের পোশাক তার পরনে। এখানকার পুরানো লোকেরা বলে, সে হচ্ছে দুর্গের প্রথমদিককার এক গভর্নর কর্নেল ওয়ারেনডারের মেয়ের প্রেতাত্মা। তরুণ অফিসারটিও তার গল্পটা জানেন। দুঃখজনক ও মর্মান্তিক এক কাহিনী সেটা।
১৬৬৭ সালে দুর্গটি নির্মাণের অল্প পরেই এর গভর্নরের দায়িত্ব পান কর্নেল ওয়ারেনডার। আইন-কানুন এবং নিজের কর্মচারী-সৈনিকদের বিষয়ে কঠোর ছিলেন খুব। তবে একই সঙ্গে মেয়ে উইলফুলকে খুব ভালবাসতেন। স্যর ট্রেভর অমহার্সট নামের অভিজাত এক তরুণকে ভালবাসত উইলফুল। দু’জনেই একে অপরকে বিয়ে করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। কর্নেলও উপযুক্ত এক তরুণকে বেছে নেয়ায় মেয়ের প্রতি খুব সন্তুষ্ট ছিলেন।
গ্রীষ্মের এক বিকালে জমকালোভাবে, অনুষ্ঠিত হলো তাদের বিয়ের অনুষ্ঠান। একে অপরের প্রতি গভীর ভালবাসা নিয়ে দুই তরুণ-তরুণী হাঁটতে থাকে দুর্গের পথ ধরে। এসময়ই উইলফুলের নজর যায় ফুলগুলোর দিকে
‘এই, দেখো!’ বিস্মিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল সে, দুর্গের পাথুরে দেয়ালের ওপাশ থেকে অনেক নিচে পাথরের পাশে ফুটে থাকা ফুলগুলোর দিকে আঙুল তুলল। ‘ওগুলো কী সুন্দর!’ স্যর ট্রেভরের হাতে চাপ দিল। ‘ওহ, আমি যদি ওগুলো দিয়ে বানানো একটা তোড়া পেতাম।’
দুর্গের এই প্রান্তে কর্নেল ওয়ারেনডারের রেজিমেন্টের এক তরুণ সিপাহী টহল দিচ্ছিল। উইলফুল যখন কথাগুলো বলছিল তখন পাশ দিয়ে যাচ্ছিল সে।
‘মাফ করবে, ম্যাম।’ বলল সিপাহী, ‘জায়গা ছেড়ে যাওয়ার নিয়ম নেই আমার। তবে ফুলগুলো যদি খুব ভাল লেগে থাকে, তবে নিচে নেমে ওগুলো তোমার জন্য আনতে পারি।’
‘ওহ! অবশ্যই!’ খুশিতে ডগমগ হয়ে বলল উইলফুল, ‘ধন্যবাদ! অনেক ধন্যবাদ!’
ওপর থেকে নিচের পাথরগুলো দেখল সৈনিক। তারপর নববিবাহিত দম্পতির কাছে এসে বলল, ‘তোমার স্বামীকে একটু সময়ের জন্য আমার জায়গায় পাহারায় থাকতে হবে, আমি কিছু রশি জোগাড় করে আনছি।’ পাথরের দেয়ালের গায়ে রাইফেলটা ঠেস দিয়ে রাখল সৈনিক। তারপর ইউনিফর্মের ওপর চাপানো জ্যাকেটটা খুলে ফেলল। ‘আমার মোটেই সময় লাগবে না, স্যর। কোন ঝামেলা হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। তবে পোস্ট ছেড়ে গেছি কেউ জানুক, এটা চাইছি না।’
‘ওহ, অবশ্যই।’ বললেন স্যর ট্রেভর। তারপর নিজের কোটটা খুলে গায়ে চাপালেন সৈনিকের জ্যাকেট। রাইফেলটা তুলে নিলেন হাতে। ওদিকে সৈনিকটি দ্রুতপায়ে হাঁটতে শুরু করেছে।
অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে শক্ত এক গোছা দড়ি নিয়ে হাজির তরুণ। তারপর ওই দড়ি বেয়ে সাবধানে পাথুরে দেয়ালের পাশ দিয়ে ফুলগুলোর দিকে নামতে লাগল। এদিকে স্যর ট্রেভর সৈনিকের জ্যাকেট পরে টহল দিতে লাগলেন। যখনই উইলফুলের পাশ দিয়ে যাচ্ছেন স্বামীর দিকে তাকিয়ে ফিক ফিক করে হাসছে মেয়েটা।
এই সময় সাগরে ডুব দিল সূর্যটা। সন্ধ্যাটা ক্রমেই শীতল হয়ে উঠছে। রাইফেল নিয়ে টহল দেয়ার ফাঁকে স্যর ট্রেভরের মনে হলো, রাতের বাতাসে উইলফুলের নিশ্চয়ই অনেক ঠাণ্ডা লাগছে। সৈনিকটি ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার জন্য চমৎকার একটা ফুলের তোড়া নিয়ে আসার প্রতিজ্ঞা করে উইলফুলকে দুর্গে তাঁদের কামরায় যেতে রাজি করালেন।
স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে একটা চুমু দিয়ে বিদায় জানিয়ে উঁকি দিলেন দেয়ালের ওপাশে। সৈনিকটির এত দেরি হচ্ছে কেন বুঝতে পারছেন না। তবে এখান থেকে এই অন্ধকারে নিচের জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন না। ডাক দিলেও সাগরের ঢেউয়ের শব্দের কারণে সৈনিকটি শুনতে পাবে না।
স্যর ট্রেভরের অনেক পরিশ্রম গিয়েছে আজ। অপেক্ষা করার ফাঁকে একটু বসে জিরিয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। শীতল পাথুরে দেয়ালে হেলান দিয়ে সাগরের শব্দ শুনতে শুনতে বিয়ের দিনটি এবং সুন্দরী প্রিয়তমা স্ত্রীর কথা হয়তো ভাবছিলেন। একপর্যায়ে ক্লান্তিতে দু’চোখ বুজে এল তাঁর।
স্যর ট্রেভর ঘুমিয়ে যাবার পর বেশি সময় কাটেনি। এসময় কর্নেল ওয়ারেনডার রাতের টহলে বের হয়েছেন, দুর্গের সৈনিকরা ঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছে কিনা দেখতে। আধো আলো-ছায়ায় নিজের জামাতাকে চিনতে পারলেন না কর্নেল। যখন দেখলেন ইউনিফর্ম পরা কাঠামোটা রাইফেল কোলের ওপর রেখে দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুমুচ্ছে প্রচণ্ড রেগে গেলেন।
‘সৈনিক, এই তোমার টহল দেয়ার নমুনা?’ জানতে চাইলেন কর্নেল।
ঘুমে তলিয়ে থাকা স্যর ট্রেভর নড়লেন না পর্যন্ত।
‘আমার প্রশ্নের জবাব দাও।’ চিৎকার করে বললেন কর্নেল। রাগটা ক্রমেই বাড়ছে তাঁর। এবারও স্যর ট্রেভর নড়লেন না।
কর্নেল নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি হারিয়েছেন ততক্ষণে। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করে ফেললেন মুহূর্তের মধ্যে। ‘আমার কমাণ্ডে কোন প্রহরী ডিউটির সময় ঘুমায় না।’ রাগে চেঁচিয়ে উঠেই সিপাহীর জ্যাকেটের উজ্জ্বল বোতাম সই করে ট্রিগার টিপে দিলেন। স্যর ট্রেভরের হৃৎপিণ্ড ভেদ করল তাঁর বুলেট।
কর্নেল ওয়ারেনডার যখন দেহটা পরীক্ষা করতে গেলেন তখনই ভয়াবহ ভুলটা বুঝতে পারলেন। আতঙ্কিত কর্নেল তক্ষুণি দুর্গের চিকিৎসককে আনতে লোক পাঠালেন। তবে ইতোমধ্যে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। স্যর ট্রেভর সবার ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছেন।
তার বাবা প্রিয়তম স্বামীকে মেরে ফেলেছে এটা সহ্য করা উইলফুলের জন্য ছিল অসম্ভব। যখন এটা শুনল উন্মাদ হয়ে গেল। বিয়ের পোশাকে দৌড়ে গেল সে জায়গাটায় যেখানে স্বামী বিদায় জানিয়ে তাকে শেষবারের মত চুমু খায়। পাথরের হাঁটাপথে স্বামীর রক্ত দেখে যন্ত্রণায় কেঁদে উঠল হতভাগা মেয়েটা। তারপর কেউ বাধা দেয়ার আগেই লাফ দিল দেয়ালের ওপাশে। নিচের পাথুরে দেয়ালে আছড়ে পড়ে মৃত্যু হয় তার সঙ্গে সঙ্গে।
ওই রাতেই পাপবোধ, মানসিক যন্ত্রণা ও মেয়ের পরিণতিতে স্তব্ধ কর্নেল কোয়ার্টারে নিজের কামরায় দরজা আটকে দেন। যে পিস্তল ব্যবহার করে বোকার মত বিয়ের রাতে মেয়েকে বিধবা বানান সে পিস্তলের গুলিতে আত্মাহুতি দেন নিজেও।
গত কয়েক শতকে তরুণী এই কনের প্রেতাত্মাকে দেখা গিয়েছে বহুবার। যে কামরাটা তাদের জন্য বরাদ্দ ছিল সেখানে এবং যে পথে শেষ সময়টা কাটিয়েছে প্রিয়তমের সঙ্গে সেখানেই ফিরে ফিরে আসতে দেখা যায় উইলফুলের প্রেতাত্মাকে। কখনও কখনও খুব রাগী দেখায় তার চেহারা। তবে বেশিরভাগ সময় দুঃখী, হতাশাগ্রস্ত এক নারীর প্রতিমূর্তি হয়েই হাজির হয়।
ওই রাতে ছোট্ট ছেলেটার কবজি স্পর্শ করার কারণ সম্ভবত বাবার বোকামি আর হিংস্রতার কারণে যে পরিবারের স্বাদ সে পায়নি তার আকাঙ্ক্ষা। আদর্শ এক স্ত্রী এবং মা হবার স্বপ্ন বুকে নিয়েই মারা যায় দুর্ভাগা মেয়েটা। তার বদলে সে কিনা হলো কিনসেল ফোর্টের শ্বেতবসনা প্রেতিনী।
কিনসেল দুর্গের শ্বেতবসনা প্রেতাত্মার গল্প আসলে এক কিংবদন্তী। উইলফুল ওয়ারেনডারের ভূতই যে সে এ ব্যাপারে নিশ্চিত কোন তথ্য-প্রমাণ নেই। তবে বিগত বছরগুলোতে যারাই তাকে দেখেছে একই বর্ণনা দিয়েছে, সাদা বিয়ের পোশাকের এক তরুণী। অনেক উচ্চপদস্থ সামরিক কর্তাসহ অজস্র মানুষ এই ভূত দেখেছে। নিয়মিত হাজির হওয়া প্রেতাত্মার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই প্রেতিনী।
সাগরের ভুতুড়ে কাণ্ড
সাগরে ঘটে নানা ধরনের ভুতুড়ে কাণ্ড-কীর্তি। ভুতুড়ে জাহাজ, প্রেত, দৈব ভবিষ্যদ্বাণী, নাবিকের অতৃপ্ত আত্মা এমন আরও কত কী!
ভয়ানক ভবিষ্যদ্বাণী
এখন যে ঘটনাটি বর্ণনা করব আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভবই মনে হতে পারে আপনার কাছে। কিন্তু এর প্রত্যেকটি অংশই খুব ভালভাবে নথিবদ্ধ করা হয়েছে। তাই স্বীকার করে নিতে হবে সত্য কখনও কল্পনাকেও হার মানায়।
একসময় ‘আস্ক’-এর ক্যাপ্টেন ছিলেন রিচার্ড ব্রাউন। ১৮৬০-এর দশকের এক ভ্রমণের ঘটনা। কেবিনে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন ব্রাউন। এখন পর্যন্ত এবারের যাত্রায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। ক্যাপ্টেনের অধীনে বিশ্বস্ত কিছু ক্রু কাজ করছে। এমনিতে বেশ সাদাসিধে মানুষ ব্রাউন। সাগর, ক্রু আর নিজের জাহাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারলেই খুশি।
একমুহূর্ত পরেই তাঁর ফুট তিনেক সামনে এক নারীমূর্তিকে দেখতে পেলেন। যদিও নারীটির শরীর ভেদ করে সাগরটাও দেখা যাচ্ছে। মাথা ঝাঁকিয়ে, চোখ কচলে আবার তাকালেন ব্রাউন। তখনই শরীরে শীতল একটা স্রোত বয়ে গেল। বুঝতে পারলেন আর যা-ই হোক, এ রক্তমাংসের কোন মানুষ নয়।
ছায়ামূর্তির আরও কাছাকাছি হলেন উঠে দাঁড়িয়ে। পরে বলেছিলেন কীভাবে যেন অতিপ্রাকৃত এই শক্তির বশে চলে এসেছিলেন।
‘এখনই জাহাজটা ঘুরিয়ে ফেলো,’ দুর্বল কণ্ঠে বলল সে, ‘বাড়ির দিকে ফিরে চলো। এই জাহাজটা অশুভ। যদি ফিরিয়ে না নাও তোমার সব ক্রুকেই হারাবে, যাবে নিজের জীবনটাও।’
সতর্কসঙ্কেত দিয়ে একমুহূর্ত দেরি না করে অদৃশ্য হলো অশরীরী I
কয়েক মিনিটের জন্য যেন নড়াচড়ার শক্তি হারিয়ে ফেললেন ক্যাপ্টেন ব্রাউন। একের পর এক প্রশ্ন তৈরি হচ্ছে মনে। আমার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে? ওই জিনিসটাকে থোড়াই কেয়ার না করে কোর্স ধরেই চলতে থাকব? নাকি ভুতুড়ে ওই সতর্কবাণী মাথা পেতে নিয়ে জাহাজ ঘোরাব?
শেষ পর্যন্ত মালিকদের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন ব্রাউন। ক্রুরা অবাক হলেও বুঝতে পারল নিরাপত্তার ব্যাপারে আশঙ্কা তৈরি হওয়ায়ই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ক্যাপ্টেন। আদেশ মেনে জাহাজের কাজ করতে লাগল তারা। ক্রুরা এটাও জানে মাল নির্দিষ্ট বন্দরে না পৌঁছে দিয়ে ফিরে গিয়ে নিজের ক্যারিয়ার শেষ করছেন ক্যাপ্টেন।
ওয়ালসের কার্ডিফ বন্দরে যখন ভিড়ল জাহাজ যা প্রতিক্রিয়া হওয়ার তাই হলো। ব্রাউনকে বহিষ্কার করা হলো, সেই সঙ্গে তাঁর জাহাজ চালানোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হলো। কয়েক বছর বাদে ভেঙে পড়া ও বিধ্বস্ত অবস্থায় মৃত্যু হয় ব্রাউনের।
এদিকে আস্ক কিন্তু ঠিকই মালিকের নির্দেশনায় যাত্রা চালিয়ে গেল। দ্রুত যোগ্য একজন ক্যাপ্টেন নিয়োগ পেলেন। নতুন সব ক্রু নিয়ে চলল জাহাজটি পুরানো গন্তব্যের উদ্দেশে, যেটা ওই ভুতুড়ে ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে বানচাল হয়। কয়েক হপ্তা বাদে জাহাজের মালিকরা একটা খবর পেলেন। আটলান্টিক মহাসাগরে দেখা গেছে আস্ককে, যেখান থেকে ব্রাউন জাহাজ ঘুরিয়েছেন তার কাছেই। আগুনে গোটা জাহাজটাই পুড়ে ছারখার। ক্রুরা সবাই এখনও জাহাজেই আছে, তবে কেউ বেঁচে নেই।
প্রেতাত্মার ভবিষ্যদ্বাণী ঠিকই ছিল। জাহাজের মালিক, নতুন ক্রু এবং ব্রাউনের দুর্ভাগ্য-দেরি হয়ে যাওয়ার আগে কেউই বিষয়টি বুঝতে পারেনি।
নাবিকের সমাধি
কখনও কখনও অতিপ্রাকৃত কোন সংবাদও ছাপা হয় পত্রিকার পাতায়। এবারের ঘটনাটি ছাপা হয় ১৯২১ সালের ১২ মে রচেস্টার ডেমোক্রেট অ্যাণ্ড ক্রনিকল পত্রিকায়।
ওই সময় লেক ওন্টারিওর তীরবর্তী এলাকাগুলো ছিল অনেকটাই লোকবসতিহীন। হঠাৎ হঠাৎ আদিবাসীদের একটা-দুটো ছোটখাট বসতি বা বাড়িঘর চোখে পড়ত। ইয়োরোপীয়দের পদধূলি কমই পড়ত সেখানে। তবে সন্দেহ নেই ওখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কোন তুলনা হয় না।
আবার প্রকৃতির রুদ্ররূপের কারণে ১৮০০ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত এখানে বেশ কিছু মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে। ১৮৫৭ সালের এক ঝড়ের সময় জলে ডুবে মৃত্যু হয় এক নবিকের। নিউ ইয়র্কের সোডাস বে-র পয়েন্ট চার্লসের তীরে সমাহিত করা হয় তাকে। এদিকে বিংশ শতকের গোড়ার দিকে চমৎকার সব বিলাসবহুল কটেজ তৈরি হতে থাকে এলাকাটিতে। এরকম কিছু কটেজের মালিক মিলে একটা সংগঠন দাঁড় করান। গ্রীষ্মকালীন এই আবাসস্থলগুলোর আশপাশের এলাকা রক্ষণাবেক্ষণ এবং দেখভালের জন্য একজন কেয়ারটেকারও নিয়োগ করেন তাঁরা। ১৯১৭ সালের দিকে এখানকার কেয়ারটেকার ছিল জর্জ কারসন নামের এক ব্যক্তি।
এই এলাকার সঙ্গে বেশ ভালমতই পরিচিত ছিল কারসন। তার জানা ছিল, সোডাস উপসাগরে যখন শক্তিশালী উত্তর-পুব বায়ু বয়ে যায় তখন কটেজগুলোর কাছে গোর দেয়া ওই নাবিকের কান্না শুনতে পাওয়া যায় বলে দাবি করে এখানকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা। এসব বিষয়ে কারসনের চিরকালের অবিশ্বাস। বাতাসের শব্দই এর জন্য দায়ী এ বিষয়ে সন্দেহ নেই তার মনে। লোকেদের কল্পনাই একে অন্য দিকে নিয়ে গেছে।
একপর্যায়ে মারফি পরিবারের সদস্যরাও কারসনকে জানায় প্রচণ্ড এক উত্তর-পুর ঝড়ের সময় একটা ভূত তাদের দেখা দেয়। এমনিতে মারফিদের পছন্দ করে এবং বিশ্বাসও – করে কারসন। কিন্তু ওই গ্রীষ্মের রাতে তাদের যে অভিজ্ঞতা হয় বলে দাবি করেছে তা হেসেই উড়িয়ে দেয় সে। পরিবারের সদস্যরা জানায় ডাইনিং রুমের টেবিলে বসে ছিল সবাই। এসময় কটেজের দেয়ালের বাইরে থেকে নক করার শব্দ শুনতে পায়। মি. মারফি প্রতিটি জানালা পরীক্ষা করেও এ ধরনের কোন শব্দের কারণ খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হন। কাউকে দেখেনওনি।
শব্দটা হতেই থাকলে ছেলে-মেয়েদের চুপচাপ থাকার নির্দেশ দেন ভদ্রলোক। প্রথমে ভাবলেন কোন প্রতিবেশী ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। কিন্তু দশ মিনিট ধরে অনবরত আওয়াজটা হতেই থাকলে বিষয়টা কী তদন্ত করে দেখবেন স্থির করেন। ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসেন মারফি এবং তাঁর সন্তানেরা। অর্ধেক গেল বামে। বাকি অর্ধেক ডানে। একপর্যায়ে আবার সামনের দরজায় একত্রিত হলো সবাই। অস্বাভাবিক কিছু দেখা যায়নি, যেমন খুঁজে বের করা যায়নি শব্দের কারণ।
ছোট বাচ্চাদুটি ভেতরে চলে গেল। এদিকে মারফি বড় ছেলেটাকে নিয়ে ঘরের চারপাশে তল্লাশি চালিয়ে যেতে লাগলেন। যদি এই ঠক ঠক আওয়াজের ব্যাপারে কোন সূত্র মেলে। শোঁ শোঁ শব্দে ঝড়ো বাতাস বইছে। এরই মধ্যে ধৈর্য নিয়ে খুঁজছে দু’জনেই। হঠাৎই চোখে পড়ল বেশ কিছুটা নিচে লেকের পাড়ে তুমুল বাতাসের মধ্যে বসে আছে ভৌতিক একটি আকৃতি। বাপ-বেটার ভয়ার্ত দৃষ্টির সামনে কাঠামোটা উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে হাঁটতে পুরানো সেই নাম না জানা নাবিকের সমাধিটার সামনে হাজির হলো। হাতদুটো ওপরে তুলল, তারপর অদৃশ্য হলো।
রাতে পরিবারের একজনেরও ভাল ঘুম হলো না। তবে একেবারে সকাল সকাল উঠে পড়ল সবাই। দুপুরের মধ্যে পাথর দিয়ে একটা স্মৃতিফলক তৈরি করে সমাধিতে স্থাপন করল। আশা করল এর ফলে হয়তোবা পরের বার উত্তর-পুব ঝড় বইলেও পরিবারটিকে আর বিরক্ত করবে না প্রেতাত্মাটা।
ওই গ্রীষ্মেই মারফিদের জমিতে টহল দেয়ার সময় অসাবধানতাবশত পা লাগিয়ে এত যত্নে গড়া পাথরের ফলকটা উপড়ে ফেলল জর্জ কারসন। অন্যান্য আবর্জনার সঙ্গে পাথরের টুকরোগুলো কটেজের পেছনের ময়লার স্তূপে ফেলে দিল।
ওই দিন সন্ধ্যায় রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষে চাঁদের আলোয় টহল দিচ্ছিল কারসন। মারফিদের বাড়ির কাছাকাছি যখন পৌছল হঠাৎ একটা নড়াচড়া মনোযোগ আকর্ষণ করল। আরও ভালভাবে তাকাল। খুব বেশি দূরে নয়, যেখানে পাথরের ফলকটা উপড়ে ফেলেছে সেখানে অদ্ভুত এক দৃশ্য অপেক্ষা করছে তার জন্য। পুরানো ধাঁচের নাবিক– পোশাক পরিহিত এক ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। তবে আর যা-ই হোক, মানুষ নয়। কারণ ওটার শরীর ভেদ করে ওপাশের জলের রেখা দেখতে পাচ্ছে কারসন।
এভাবে প্রেতাত্মাটার মুখোমুখি হয়ে যাওয়ার পর আর কোন অবিশ্বাস রইল না কারসনের। পত্রিকার একজন রিপোর্টারকে সে বলে, মারফিদের বেঞ্চ আর সমাধিটার মাঝখানে প্রেতাত্মাটাকে দেখার পর ভয়ে নড়তে ভুলে গিয়েছিল। একপর্যায়ে তার চোখের সামনেই কাঠামোটা অদৃশ্য হয়ে যায়।
একমুহূর্ত দেরি না করে নিজের কেবিনে ফিরে যায় জর্জ কারসন। সে বুঝতে পারে পরের দিন সকালে তার প্রথম কাজ হলো একজন লোক ডেকে ওই পাথরের ফলকটা আবার আগের জায়গায় ঠিকমত স্থাপন করা।
আর সামান্য এই শ্রদ্ধা জানানোটাই প্রেতাত্মাটার জন্য যথেষ্ট ছিল। কারণ এরপর আর ওই ছায়ামূর্তিকে রাত- বিরেতে হাজির হয়ে চমকে দিতে দেখা যায়নি লোকজনকে। অন্তত পত্রিকাটির রিপোর্টে তা-ই বলা হয়েছিল। অবশ্য এরপরে সেখানে আর কোন ভৌতিক ঘটনা ঘটেও থাকতে পারে। কারণ ওই রিপোর্টের পর পেরিয়ে গেছে প্রায় একশো বছর।
প্রেতাত্মার সাহায্য
কখনও কখনও ছোট্ট কোন নৌকায় চেপে একাকী দুঃসাহসী সাগরযাত্রায় বেরিয়ে পড়ার খবর কানে আসে আমাদের। আমেরিকার ফ্লোরিডার বব ফ্লাওয়ার এমনই একজন। ১৯৭৮ সালের গ্রীষ্মে তার আঠারো ফুটি নৌকাটা নিয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলো ফ্লাওয়ার। মিসকিটার নামের নৌকাটিতে চেপে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিতে বদ্ধপরিকর সে। এবারের অভিযানটা সফল হলে মিসকিটারকে নিয়ে বিশ্বভ্রমণে বেরোনোর পরিকল্পনা।
যেদিন সাগরে নামাল নৌকাটিকে, সব কিছু ছিল চমৎকার। আকাশটা পরিষ্কার, সূর্য দারুণ আলো ঝরাচ্ছে। আটলান্টিক মহাসাগর এতটাই শান্ত যে ফ্লাওয়ারের মনে কোন শঙ্কাই রইল না। রাতের বেলা হঠাৎই পরিবেশ পাল্টে গেল। বাতাস ও ঢেউ তার ছোট্ট নৌকাটিকে নিয়ে রীতিমত খেলতে শুরু করল। নৌ বিদ্যা সম্পর্কে জানা সব ধরনের জ্ঞান প্রয়োগ করেও ঝড়ের সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে পারছিল না ফ্লাওয়ার। কোন একটা অলৌকিক ঘটনা ঘটা ছাড়া আর রক্ষা নেই বুঝতে পারল।
একটার পর একটা দিন পেরোতে লাগল। ঝড় থামার কোন লক্ষণ নেই। ফ্লাওয়ারের রীতিমত কাহিল অবস্থা। ঝড় এতটাই প্রবল যে বড় জাহাজগুলোও মিসকিটারকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসতে পারল না।
পুরোপুরি হাল ছেড়ে দিয়েছে ফ্লাওয়ার। কেবলমাত্র বেঁচে থাকার চেষ্টা করা ছাড়া আর কিছুই করছে না এখন। বাঙ্কের সঙ্গে দড়ি দিয়ে শরীরটা বাঁধল, যেন সাগরে পড়ে না যায়।
একপর্যায়ে জ্ঞান হারাল। টানা ৯০ ঘণ্টা পর জেগেছিল। কতক্ষণ পর বলতে পারবে না হঠাৎ কেবিনে একটা কণ্ঠ শুনতে পেল। কী হচ্ছে কিছুই বুঝতে পারল না। চোখ খুলতেই কেবিনে তিনজন মানুষকে দেখতে পেল। দেখে অভিজাত কোন প্রমোতদরীর যাত্রী বলে মনে হলো।
ফ্লাওয়ার ভাবল প্রবল খিদে, ভয়, পিপাসা আর ক্লান্তিতে হ্যালুসিনেশন হচ্ছে তার। চোখ বন্ধ করে দেয়ালের দিকে মুখ ফেরাল। এরই মধ্যে ওই তিনজন লোকের কথা শুনতে পাচ্ছে।
‘আমাদের কি একটা পাল টানানো উচিত?’ একজন জানতে চাইল। তারপর নানা ধরনের যুক্তি দেখাতে লাগল তিনজন। তবে এর সব কিছুই কীভাবে বব ফ্লাওয়ারকে সাহায্য করা যায় তা নিয়ে। তারা একটা বিষয়ে নিশ্চিত, ফ্লাওয়ার নিজের জীবন বাঁচাতে পারবে না। এই অপমানটা গায়ে না মাখার সিদ্ধান্ত নিল বাঙ্কে শায়িত তরুণ। সে বারবার নিজেকে বোঝাতে লাগল গোটা বিষয়টাই তার কল্পনা।
তবে যতই সময় গড়াল এই অবিশ্বাসী মনোভাব বজায় রাখা কষ্টকর হয়ে পড়ল। কারণ ওই লোকগুলো তাকে তুলে নানা ধরনের পরামর্শ দিতে লাগল জাহাজ নিয়ে। তাদের কথার কোন আগামাথা পাচ্ছে না সে। একপর্যায়ে ভাবতে আরম্ভ করল, ঝড়, না এই লোকগুলো তার প্রধান শত্রু?
এই অদ্ভুত লোকগুলোর কথামতই নৌকাটা পরিচালিত করল ফ্লাওয়ার। তারপর বিধ্বস্ত অবস্থায় শুয়ে পড়ল কেবিনে আবার। একটু পর লোকগুলোর একজন এসে তাকে মিসকিটারের ডেকে যাওয়ার নির্দেশ দিল।
‘তোমার ফ্লেয়ার গানগুলো জ্বালো। কাছেই একটা জাহাজ আছে। ওটাই তোমাকে বাঁচাবে।’
কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে কয়েকটা ফ্লেয়ার গান ছুঁড়ে মারল আকাশে। তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল ডেকের ওপর। একটু পরেই একটা মালবাহী জাহাজকে দেখা গেল দৃষ্টিসীমায়।
কয়েক সেকেণ্ড পর আবারও কোনমতে শরীরটাকে টেনে নিয়ে কেবিনে ঢুকল। ওই তিন আগন্তুক অদৃশ্য হয়েছে। একটু পরই ফ্লেয়ার গানের আলো দেখে হাজির হওয়া জাহাজটা মিসকিটার এবং এর মালিককে উদ্ধার করে বন্দরে নিয়ে গেল।
কয়েক মাস পর যখন তার সাক্ষাৎকার নেয়া হয় তখন বিষয়টা নিয়ে আবার সন্দেহের দোলাচলে ভুগতে থাকে সে। যদিও কথা থেকে যায়। সে কীভাবে বুঝল তখনই ফ্লেয়ার গান ছুঁড়তে হবে?
সব কিছু মিলিয়ে অতিপ্রাকৃত রহস্যের ইঙ্গিতই পাই আমরা। অন্য ভুবনের তিনজন মানুষ তাকে সাহায্য করেছে নাকি ওই পরিস্থিতিতে তার মনের মধ্যে এমন একটা ক্ষমতা তৈরি হয় যাতে সে বুঝতে পারে একটা জাহাজ এগিয়ে আসছে, সে রহস্যের সমাধান হয়নি আর
ভুতুড়ে জাহাজ
নিস্তব্ধতা, স্থিরতা ও অন্ধকার এই তিনটা অ্যানি এম. রেইড নামের জাহাজটির ক্রুদের সেদিন আঁকড়ে ধরেছিল। ক্যাপ্টেন ডার্কি নোঙর ফেলতে ও পাল গোটাতে বললেন। চারপাশের পরিবেশে একটা অস্বাভাবিক কিছু টের পাচ্ছিল নাবিকরা। কেউ কথা বলছে না। উত্তমাশা অন্তরীপ পেরোনোটা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে এটা তাদের জানাই ছিল। এই জায়গাটা তারা দ্রুত পেরিয়ে যেতে পারলেই শান্তি পেত। এর বদলে এখন এমন নিস্তব্ধতার মধ্যে অপেক্ষা করাটা নিশ্চয়ই প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করছে নাবিকদের মনে।
অস্বাভাবিক নীরবতা, গাঢ় অন্ধকার এবং ভুতুড়ে এই স্থিরতার সঙ্গে কিছুটা মানিয়ে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন ডার্কির মনে হলো চারপাশে একটা পরিবর্তন অনুভব করতে এবং দেখতে পাচ্ছেন। ‘আমার মন কি আমাকে ধোঁকা দিচ্ছে?’ নিজেকে প্রশ্ন করলেন। কিন্তু ডার্কি সাগর সম্পর্কে খুব অভিজ্ঞ এক মানুষ। নিজেকে শান্ত করলেন। জাহাজ এবং এর নাবিকদের নিরাপত্তা নির্ভর করছে তাঁর ওপর। স্পাইগ্লাসটা চোখে দিয়ে চারপাশের অন্ধকারের রাজ্যে কিছু ঠাহর করা যায় কিনা বোঝার চেষ্টা করছেন।
ওখানে ওটা কী? চমকে উঠলেন। ফুট পঞ্চাশেক দূরে সাগরের পানিতে একটা আলোড়ন দেখা যাচ্ছে।
কয়েক সেকেণ্ড পরেই চারপাশে একটা শীতল ঘূর্ণি বাতাসের উপস্থিতি টের পেলেন। এদিকে সাগরের ওই অংশটার পরিস্থিতিও যেন আস্তে আস্তে বদলাচ্ছে। ধূসর একটা কুয়াশা তৈরি হয়েছে সেখানে। আশ্চর্য একটা বিষয় নজরে পড়ল তাঁর টেলিস্কোপ, গ্লাসটায় চোখ লাগাতেই। কুয়াশা স্বচ্ছ হয়ে গিয়ে ওপাশে আরেকটি জাহাজের অবয়ব ফুটিয়ে তুলেছে। ধীরে ধীরে এদিকেই এগিয়ে আসছে।
ক্যাপ্টেন উন্মত্তের মত চিৎকার করে নাবিকদের একের পর এক নির্দেশ দিতে লাগলেন। নাবিকরা ত্বরিত সাড়া দিল। ডেকের সতর্কতামূলক নীল বাতি জ্বেলে দেয়া হলো। ছোট্ট জাহাজটা এখন এত কাছাকাছি চলে এসেছে যে, খালিচোখেও দেখা যাচ্ছে। ওখানকার কেউই মনে হয় এখনও অ্যানি এম. রেইডকে দেখতে পায়নি। ওই জাহাজের ক্যাপ্টেন বা নাবিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পারলে কপালে খারাপি আছে বুঝতে বাকি রইল না ডার্কির।
এগিয়ে আসা ছোট্ট কার্গো জাহাজের নাবিকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য রেইডের লোকেরা ডেকের ওপর লাফাতে লাগল, পতাকা নাড়াচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে। কিন্তু ওটা সেই আগের মতই এগিয়ে আসছে।
‘পাল তোলো। একটা দমকা বাতাস আসছে। এটার সাহায্য নিয়ে জাহাজটা পৌছার আগেই হয়তো দূরে সরে পড়তে পারব।’ হুকুম দিলেন ক্যাপ্টেন ডার্কি।
দ্রুতই বাতাসটা এল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে হিমশীতল ওই বাতাসটার ঝাপটা লাগল জাহাজে। এদিকে কার্গো জাহাজটা গায়ের ওপর উঠে এসেছে। সংঘর্ষ অনিবার্য। রেইডের প্রত্যেকটি নাবিক বুঝে গেল তাদের কেপ অভ গুড হোপের সৌভাগ্যের সমাপ্তি ঘটতে চলেছে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঘটতে যাওয়া প্রচণ্ড সংঘর্ষের জন্য নিজেদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করার চেষ্টা করলেন ক্যাপ্টেন এবং নাবিকরা।
ঘন একটা কুয়াশার চাদরে নিজেকে মুড়ে অ্যানি এম. রেইডের পোর্ট বো-র গায়ে প্রায় লেগে এল জাহাজটি। তিন মাস্তুলের জাহাজের সব ক্রু অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছে তাদের আঘাত করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে থাকা জাহাজটির দিকে। ওটা যতই কাছে আসছে বাতাস আরও শীতল হচ্ছে। ডার্কির কিছু ক্রু চেঁচিয়ে উঠল যখন আপাত জনমানবহীন, জরাজীর্ণ জাহাজটি তাদের মাঝখানে কেটে চলে গেল। যেন বা এখানে অ্যানি এম. রেইড কিংবা এর নাবিকদের কোন অস্তিত্বই নেই।
পুরানো এই মালবাহী জাহাজটা আসলে আর কিছু নয়, এক ভুতুড়ে জাহাজ, নিশ্চিতভাবেই অন্য কোন সময়চক্র থেকে এখানে হাজির হয়েছিল। ওই ভুতুড়ে জাহাজ যখন সাগরে সত্যিকার অর্থেই চলত তখন হয়তো অ্যানি এম. রেইড তৈরিই হয়নি।
ভয়াবহ ওই জাহাজটি শরীরের হাড়মজ্জা কাঁপিয়ে দিয়ে তাদের ভেদ করে চলে যাওয়ার পর সময় নষ্ট করল না রেইডের নাবিকরা। আবার যাত্রার প্রস্তুতি নিল। কেপ অভ গুড হোপের এখানটায় যেভাবে বাতাস বওয়া স্বাভাবিক আবার সেভাবে বইতে থাকল। এদিকে জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং নাবিকরা প্রচণ্ড পরিশ্রম করে রেকর্ড টাইমে পৌঁছে গেল, বন্দরে।
ক্যাপ্টেন ডার্কি পরে বলেন, ‘ওটার ডেক কিংবা ব্রিজে জীবিত কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। নজরদারির জন্য লুকআউটেও ছিল না কেউ। আমরা সংঘর্ষ এড়াবার জন্য সব কিছুই করেছিলাম। খুব দ্রুতই পালগুলোও টাঙিয়ে ফেলেছিলাম।’
ক্যাপ্টেন যদি আরও বেশি কুসংস্কারাচ্ছন্ন হতেন তবে এই ঘটনার ব্যাখ্যা দাঁড় করানো মোটেই কঠিন হত না তাঁর জন্য। ১৯১১ সালে ঘটনাটি ঘটে, হ্যালোইনের সময়।
বাবা ও মেয়ে
সাউথ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যের সীমানায় পড়লেও ভৌগোলিক দিক থেকে জর্জিয়ার সাভানার কাছে হিলটন হেড দ্বীপের অবস্থান। জায়গাটি বৈরী আবহাওয়ার জন্য বিখ্যাত। জানান দেয়া ছাড়াই ঝড়ো হাওয়া বইতে শুরু করে সাগরের দিক থেকে।
একসময় হিলটন হেড আইল্যাণ্ডের বাতিঘরের রক্ষক ছিলেন এক স্ত্রী হারানো লোক। ষোলো বছরের মেয়েটা বাবার সঙ্গেই থাকত। প্রচণ্ড পরিশ্রম করতেন ভদ্রলোক। বাতিঘরের কোন অসঙ্গতিই চোখ এড়াত না। বাতিগুলোতে তেল দেয়া হত ঠিকভাবে, বাতির চারপাশের কাঁচ ঝকঝকে- তকতকে করে রাখতেন। এই দেখভালের জন্য কর্তাব্যক্তিদের খুব পছন্দের পাত্র ছিলেন এই লাইট হাউস কিপার।
সাপার শেষে প্রতি সন্ধ্যায় ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে বাতিসহ সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা ভালভাবে পরীক্ষা করে আসতেন। আবহাওয়া ভাল থাক কি খারাপ তাঁর এই প্রাত্যহিক রুটিনে কোন নড়চড় হত না। কাজেই এক ঝড়ের রাতে যখন টহল দেয়ার জন্য বেরোলেন কিপার তাঁর মেয়ে বিষয়টা নিয়ে খুব একটা চিন্তিত হলো না।
কয়েক মিনিটের মধ্যে বাতিঘরের চূড়ায় পৌঁছে গেলেন সিঁড়ি ধরে। ঝড়টা হারিকেনে রূপ নিয়েছে। বাতিগুলোর কাচের আচ্ছাদনের ওপর আছড়ে পড়ছে ঝড়ো বাতাস এবং বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টি। অভিজ্ঞ একজন বাতিঘররক্ষক হওয়ার পরও এ ধরনের ঝড় জীবনে দেখেছেন কিনা মনে করতে পারলেন না। মনে হচ্ছে শয়তান স্বয়ং যেন চড়ে বসেছে সাগর এবং বাতাসের ওপর।
ভয়ানক দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। এখানেই অপেক্ষা করে বাতি জ্বেলে রাখার চেষ্টা করবেন? নাকি সিঁড়ি বেয়ে নেমে মেয়ের কাছে যাবেন? মেয়েটা নিশ্চয়ই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছে। ঠিক করলেন দুটোই করবেন। আপাতত পোস্ট ছেড়ে গিয়ে মেয়েটার অবস্থা একবার দেখে আসবেন।
এদিকে কোয়ার্টারে মেয়েটাও বুঝতে পারছে না তার কী করা উচিত। তুলনামূলক নিরাপদ জায়গাটিতে অপেক্ষা করবে? নাকি বাবার খোঁজে যাবে? একপর্যায়ে সিদ্ধান্তে পৌছল এখানে বিশ্রাম নেয়ার আগে তাকে নিশ্চিত হতে হবে বাবা ভাল আছেন। মা মারা যাবার পর তিনিই তো তাকে আদর-ভালবাসা দিয়ে মানুষ করেছেন। অতএব আবহাওয়ার সঙ্গে লড়াই করার মত মোটামুটি ধরনের পোশাক পরে বেরিয়ে এল।
কয়েক মিনিটের মধ্যে বাবাকে খুঁজে পেল। বাতিঘরের সিঁড়ির সবচেয়ে নিচের ধাপের কাছেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। আতঙ্কিত হয়ে পড়ল কিশোরী মেয়েটা। কী করবে সে? বাবাকে কীভাবে সাহায্য করবে? এদিকে বাতিটা জ্বেলে রাখাও খুব জরুরি, ঝড়ের কবলে পড়া জাহাজগুলোকে পথ দেখাতে। বিপদ ঘটে যাওয়ার আগেই কি সাহায্য পৌঁছবে?
দুর্ভাগ্যজনকভাবে মেয়েটার মনের শেষ প্রশ্নের উত্তর ছিল না। পরিস্থিতি শান্ত হতে মোটামুটি এক হপ্তা লাগল। কেবল তখনই অনুসন্ধানী দল পাঠানো হলো বাতিঘরের রক্ষক এবং তাঁর মেয়ের অবস্থা জানতে। কংক্রিটের সিঁড়ির শেষ ধাপে পড়ে হার্ট অ্যাটাকের শিকার বাতিঘররক্ষক মারা গিয়েছেন অনেক আগেই। পরে মারা যায় তাঁর আদরের ধন একমাত্র মেয়েটিও। বাবার মৃতদেহের পাশেই পাওয়া যায় মেয়েটার নিস্পন্দ দেহ। কীভাবে সে মারা গেল এটা এক রহস্যই রয়ে যায়। বাবা-মেয়েকে ব্যক্তিগতভাবে চিনত এমন লোকদের ধারণা বাবার মৃত্যুর ধাক্কা সামলাতে না পেরেই মারা গিয়েছে মেয়ে।
আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, বাবার আত্মাটা শান্তিতেই তার শেষ গন্তব্যে চলে যায়। কিন্তু মেয়েটার আত্মা বছরের পর বছর ধরে এলাকাটাতে ঘুরে বেড়াতে থাকে। যখন তার মৃতদেহ উদ্ধার করে লোকেরা তখন যে পোশাক পরনে ছিল, পরে ওই পোশাকেই দেখা যায় মেয়েটার আত্মাকে। একটা ঝড় এগিয়ে এলে তবেই দেখা দেয় কিশোরীর প্রেতাত্মা। টাওয়ারের দিকে এগিয়ে আসা লোকেদের দিকে দৌড়ে যায় তার স্বচ্ছ কাঠামোটা। হাত নেড়ে কাছাকাছি আসতে নিষেধ করে। তারপর অদৃশ্য হয়ে যায়।
এক রাতের ঘটনা। প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস এবং বৃষ্টি হচ্ছে। এসময় বাতিঘরের ধারের রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যেতে থাকা এক দম্পতি এক কিশোরীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে রাস্তার পাশে। তাকে গাড়িতে তুলে নেয় ওই দম্পতি। গাড়ির পেছনের সিটে বসে পড়ে মেয়েটা। স্বামী যখন গাড়ি চালাচ্ছে তখন মহিলাটি পেছন ফেরে মেয়েটাকে কোথায় নামিয়ে দেবে জানতে। কিন্তু সেখানে কেউ নেই। অথচ কেবলই বৃষ্টিভেজা ওই মেয়েটাকে গাড়ির নিরাপদ আশ্রয়ে জায়গা দিয়েছে তারা। এতটাই ধাক্কা খায় ওই দম্পতি তখনই রাস্তার পাশে দাঁড় করানো হয় গাড়ি। পেছনের আসনে উঠে পড়ে ভদ্রলোক মেয়েটার খোঁজে। কিন্তু তাকে পাওয়া যায়নি। তবে পেছনের সিটের একটা অংশ ভেজা।
হতভাগা মেয়েটা ওই রাতের ঘটনায় এতটাই আঘাত পায় যে তার আত্মা শান্তি পায়নি। তবে তার এই অস্থিরতা অন্যদের জীবন বাঁচাতে সাহায্য করে আসছে মর্মান্তিক ওই ঘটনার পর থেকে।
জাহাজে অশরীরী
সাগরে বিচরণ করা নাবিকেরা নানা ধরনের বিষয়কে অশুভ বা মন্দভাগ্যের সঙ্কেত হিসাবে দেখে। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রচলিত বিষয়টি হলো, কোন জাহাজে যদি প্রেত বা ভূত দেখা যায় ওই জাহাজটির আর ভাল কোন কিছুই ঘটবে না। যখন কোন একটা জাহাজের গায়ে ভুতুড়ে তকমা লাগে তখন কোন নাবিকরাই এতে কাজ করতে চায় না। এমনকী কখনও কখনও এ ধরনের জাহাজকে বেশ নতুন এবং আরও বহু বছর সাগরে চলাচলের উপযোগী থাকার পরও ধ্বংস করে দিতে হয়েছে মালিককে।
এবার আমরা যে জাহাজটির কাহিনী শোনাতে যাচ্ছি তার নাম পনাটিক। ওটার হোম পোর্ট ছিল ইংল্যাণ্ডের লিভারপুল। ১৮৬৩-র আগ পর্যন্ত এখান থেকে দক্ষিণ আমেরিকার বিখ্যাত বন্দরগুলোয় নিয়মিতই যাওয়া-আসা করত। বেশ কয়েক বছর এই সাগরযাত্রাগুলো চলে নির্বিঘ্নে। তো একবার ফিরতি যাত্রার সময় ক্যাপ্টেন আবিষ্কার করেন তাঁর জাহাজে লোক সঙ্কট আছে। লিভারপুলের উদ্দেশে রওয়ানা হওয়ার আগে কয়েকজন লোক নিয়োগ দেয়া জরুরি। পেরুর ক্যালাওয়ের ডকগুলোতে ঘুরে তিনজন লোক পেয়ে গেলেন যাদের পছন্দ হয়েছে তাঁর, আবার তারাও কিছু আয়- রোজগারের সুযোগ হাতছাড়া করল না। ক্যাপ্টেন নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবলেন, ‘যাক, বাবা, এবার আর যাত্রা করতে কোন সমস্যা হবে না। ভ্রমণটাও মনে হয় ভালই হবে।’
কিন্তু পরের দিন আর রাতগুলো প্রমাণ করল ক্যাপ্টেনের অনুমান সম্পূর্ণ ভুল। এক পরিষ্কার, চন্দ্রালোকিত রাতে ঘটনার শুরু। বেশিরভাগ নাবিক ঘুমিয়ে আছে। কেবল পনাটিকের সবচেয়ে অভিজ্ঞ দু’জন ক্রু জাহাজকে ঠিক পথে পরিচালনার দায়িত্বে আছে। তাদের একজন উইলিয়াম, ডেকে রুটিন টহল দিচ্ছে। এসময় হুইলে থাকা এডমণ্ড রক্ত জল করা কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল।
সঙ্গে সঙ্গে টহল বাদ দিয়ে উইলিয়াম যত দ্রুত সম্ভব তার সঙ্গী যেখানে আছে সেদিকে ছুটল। ঘটনাটা কী জিজ্ঞেস করার আগেই এডমণ্ড চিৎকার করতে লাগল, ‘একটা লোক, জাহাজে একটা লোক!’
সে চোখ বড় বড় করে যেদিকে তাকিয়ে আছে সেদিকে অস্বাভাবিক কিছু নজরে পড়ল না উইলিয়ামের। একবার ভাবল সে কি তবে কোন মস্করা করল?
‘একটা লোককে তো তুমি দেখতেই পার। জাহাজে একজন নয় অনেকেই আছে। এমনকী নতুন লোকও তোলা হয়েছে। এদের সবাইকে তুমি ভালমত চেন, এডমণ্ড।’ এই বলে হেসে উঠল। ভাবল তার সঙ্গী যদি মজা করে থাকে তবে তারও একটু ঠাট্টা করতে দোষ কোথায়!
‘উইল, আমি যাকে দেখেছি সে আমাদের কোন ক্রু নয়। ভয়াবহ এক জিনিস ওটা। আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। ডেকের এক গজ ওপরে, আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল। চোখগুলোও স্বাভাবিক ছিল না। মনে হচ্ছিল অশুভ, ভয়ঙ্কর একটা কিছু ছিল ওগুলোতে।’ কাঁপতে কাঁপতে বর্ণনা দিল এডমণ্ড।
এডমণ্ডের বর্ণনা আর কাঁপা কণ্ঠস্বর শুনে উইলিয়াম বুঝতে পারল মোটেই ঠাট্টা করছে না তার সঙ্গী। একটা অতৃপ্ত আত্মা জাহাজে হাজির হয়েছে এটা বুঝে নিতে কষ্ট হলো না তার। অভিজ্ঞ দুই নাবিকের জানা আছে লক্ষণটা মোটেই শুভ নয়। মুখহীন, জ্বলতে থাকা দুই চোখের হুড পরা এক কাঠামো ওটা, যেটা আরও বেশি ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত বহন করছে। নিশ্চিতভাবেই মৃত কোন মানুষের আত্মা। দুর্যোগ ঘনিয়ে আসছে!
তাদের চিৎকার ও উচ্চস্বরে আলাপ জাহাজের বেশিরভাগ ক্রুকে জাগিয়ে দিল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে এই ভুতুড়ে অবয়ব দেখা যাওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়ল গোটা জাহাজে।
হৈ চৈ, চিৎকার ধীরে ধীরে একটু কমে আসতে শুরু করেছে, এসময় জাহাজের সবচেয়ে কমবয়স্ক নাবিকটি পিঠে একটা স্পর্শ টের পেল। ধীরে ধীরে মাথা ঘোরাল সে। যদি ভাবত তার কোন সিনিয়র সহকর্মী আশ্বস্ত করার জন্য হাত দিয়েছে পিঠে তাহলে হতাশ হতে হত তাকে। কারণ তার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে হুড পরা লম্বা এক ছায়ামূর্তি। চিৎকার করার চেষ্টা করল তরুণ, আতঙ্কে শব্দ বেরোল না গলা থেকে। ভয়ার্ত চোখে নিঃশব্দে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল কালো আলখেল্লা গায়ে চাপানো ছায়ামূর্তিটা ধীরে ধীরে দূরে সরে পড়তে লাগল। ওটার কমলা জ্বলজ্বলে চোখজোড়া এখন কেবল নজরে পড়ছে তরুণের। তার আতঙ্ক যখনই চরম শিখরে পৌঁছল সাগরের শীতল বাতাসে অদৃশ্য হলো ছায়ামূর্তি।
তবে পরের দুই দিন ও রাতে ভয়ঙ্কর কোন ঘটনা ঘটল না। জাহাজও লিভারপুল বন্দরে ভিড়ল। কোন ক্রুরই মানসিক অবস্থা ভাল নেই। তবে ভয়াবহ ওই অশরীরী চেহারা দেখানোর পরও যে তারা বেঁচে ফিরতে পেরেছে এজন্য ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল তারা।
একমুহূর্ত দেরি না করে জাহাজ ত্যাগ করল ক্রুরা। এদের একজনও আর ফিরল না জাহাজটিতে। এদিকে আশপাশের প্রত্যেকটা নাবিক তাদের মাধ্যমে রাতারাতি জেনে গেল পনাটিকের ডেকে অশরীরীর হানা দেয়ার ঘটনা। বহু অর্থের লোভ দেখিয়েও জাহাজের ক্যাপ্টেন আর একজন ক্রুকেও পেলেন না তাঁর জাহাজে কাজ করার জন্য।
কয়েক মাস ডকে পড়ে রইল জাহাজটি। তারপর মালিক আশা ছেড়ে দিয়ে বেশ নতুন অবস্থাতেই ধ্বংস করে ফেলার নির্দেশ দিলেন জাহাজটিকে। ওটার কাঠ, তক্তা ও বিভিন্ন ভাঙা টুকরো কিনে নিল পুরানো জিনিস কেনাবেচা করে এমন দোকানগুলো। সৌভাগ্যক্রমে অন্য কোন জাহাজ নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এগুলো কেনেনি। কারণ অশুভ কোন জাহাজের পরিত্যক্ত বস্তুর সঙ্গেও আত্মার নতুন ঠিকানায় পাড়ি জমানোর ঘটনা শোনা যায়।
কালো আলখেল্লা পরা হুড মাথার ওই অশরীরীর ভুতুড়ে কাণ্ড-কীর্তির এখানেই শেষ এটা অবশ্য বলতে পারব না আমরা। হয়তো অন্য কোন জাহাজ কিংবা কয়েকটা জাহাজে হানা দিয়ে যাচ্ছে ওটা।
মায়া হায়েনা
মায়ানেকড়ের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় আছে। কেউ কেউ বিশ্বাস করেন বাস্তবেও এদের অস্তিত্ব আছে। নাইজেরিয়ায় নেকড়ে নেই। তাই সেখানে মায়ানেকড়ে বা ওয়্যারউলফের কাহিনীও ডালপালা মেলতে পারেনি। তবে হায়েনা আছে বিস্তর। তেমনি আছে মায়া হায়েনা নিয়ে নানা কাহিনী। নাইজেরিয়ার উত্তর অংশ জুড়ে পর্বতের সারি। এ এলাকায় নানান গোত্রের লোকের বাস। এখানকার অধিবাসীরা বিশ্বাস করে, কিছু লোক জাদুমন্ত্রবলে রাত হলেই হায়েনার রূপ ধারণ করে। আর ঘটায় নানান অনিষ্ট। আজ থেকে শ’খানেক বছর আগে সেখানে অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা হয় এক ইংরেজ সরকারি কর্মকর্তার। স্টুয়ার্ট স্মিথ নামের ওই ভদ্রলোক সেখানে চাকরিসূত্রে নিয়োগ পান। ছোট্ট একটা পুলিস বাহিনীর সহায়তায় জায়গাটিতে শান্তি বজায় রাখা ছিল তাঁর দায়িত্ব। আসলে নাইজেরিয়ায় তখন একের পর এক টিনের খনির খোঁজ মিলছে। নানান জায়গা থেকে ভিড় জমাচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার, কুলি ও শ্রমিকরা। বানানো হচ্ছে রাস্তাঘাট। কুলি- মজুরদের জন্য গড়ে উঠছে একটার পর একটা বস্তি, ইঞ্জিনিয়ারদের জন্য কোয়ার্টার।
এই এলাকাটির অবস্থান বাউচি মালভূমিতে। নিচ থেকে হঠাৎ তাকালে মনে হবে এটা বুঝি বা গ্রানেট পাথরের পাহাড়। কোন লোকবসতি নেই। তবে ওপরে উঠলেই বুঝবেন কতটা ভুল করেছিলেন। সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাঠ, মাঝে মাঝে ছোট ছোট গ্রাম। দিনে প্রচণ্ড গরম, রাতে আবার কনকনে ঠাণ্ডা। বাউচি মালভূমি এলাকায় চিল, বাজ, শকুনসহ ছোট-বড় নানা ধরনের পাখির কোন লেখাজোখা নেই। সে তুলনায় বন্য জানোয়ারের সংখ্যা বেশ কম। খরগোশ, বিশাল সব ধাড়ি ইঁদুর আছে বেশ। বড় প্রাণীর মধ্যে পাহাড় ও পাহাড় পাদদেশের এলাকাগুলোয় চিতা বাঘ। তবে হায়েনা আছে অনেক। সন্ধ্যা হলেই বেরিয়ে পড়ে শিকারে। বাগে পেলে নিঃসঙ্গ পথচারীদেরও ছাড়ে না। এদের রক্ত জল করা চিৎকার অতি দুঃসাহসীদেরও বুক কাঁপিয়ে দেয়। এখানে প্রসঙ্গক্রমে এই এলাকার আদিবাসীদের একটু বর্ণনা দেয়া উপযুক্ত মনে করছি। এদের শরীরে পোশাকের খুব একটা বালাই নেই। একটা সময় শ্বেতাঙ্গদের এই এলাকায় প্রবেশ ছিল নিষেধ। বিষাক্ত তীর-ধনুক নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ত অনুপ্রবেশকারীদের উপর। তবে শ্বেতাঙ্গদের আগ্নেয়াস্ত্রের কাছে বশ মেনেছে ইদানীং।
যা হোক, স্টুয়ার্ট স্মিথের অধীনে আছে বারোজন কনস্টেবল এবং একজন কর্পোরাল। স্টুয়ার্টের সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গিয়েছে এখানে কাজ করতে আসা মাইনিং কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার অস্টারস্টকের। এক নদীর তীরে টিনের সন্ধানে খনন কাজ চালাচ্ছেন অস্টারস্টক। বিকাল হলেই দেখা যায় অস্টারস্টক হাজির হয়েছেন স্মিথের বাংলোয়। তারপর দু’জনে মেতে উঠতেন গল্প-গুজবে। এরকমই একদিন আলাপের সময় স্মিথ বললেন, ‘এখানে আসার পর একটা অদ্ভুত গুজব শুনলাম স্থানীয় অধিবাসীদের কাছ থেকে। সন্ধ্যা নামলে অন্ধকারে বেরোতে সতর্ক করে দিল তারা। বলল বেরোলেই সমূহ বিপদ। সাধারণ হায়েনার পাশাপাশি শিকারে বের হয় হায়েনা-মানবেরা। গ্রামেরই কয়েকজন লোক জাদুমন্ত্রবলে হায়েনায় রূপান্তরিত হয়। তারপরই একটা ঘটনা ঘটল। একটা কাজে বের হয়েছি। বেলা শেষ হয়ে আসায় গাঁয়ের কাছেই তাঁবু ফেলার নির্দেশ দিলাম ভৃত্যদের। রাত্রে খাওয়া শেষে শুতে যাওয়ার পরেই দুটো হায়েনা হাজির হলো তাঁবুর কাছে। ওদের চিৎকারে কান ঝালাপালা হবার জোগাড়। আমরা ঘুমালেই হামলা করার ফন্দি-ফিকির করছে মনে হয়। তাই বের হয়ে এসে দুই গুলিতে দুটোকেই মেরে ফেললাম।
‘ভোরে ঘুম ভাঙল এলাকাবাসীর চেঁচামেচিতে। রাতের ঘটনা তারা জানতে পেরেছে। লোকগুলোর ধারণা এই হায়েনাদুটো আসলে হায়েনা-মানব। তারা তাদের গাঁয়েরই লোক। আমি হেসে উড়িয়ে দিলাম লোকগুলোর কথা। কিন্তু
মানল না। এবার বোঝানোর চেষ্টা করলাম। তাতেও কাজা হলো না। সকালবেলা যখন সবার ঘুম ভাঙল গাঁয়ের লোকেরা মাথা গুনে আবিষ্কার করল সবাই আছে। এবার কিছুটা নিশ্চিন্ত হলো। তবে গোঁ ধরল হায়েনাদুটো কাছের অপর কোন গ্রামের লোক।’
স্মিথ ভেবেছিলেন তাঁর কথা শুনে অস্টারস্টকের পিলে চমকে উঠবে। তাঁকে অবাক করে দিয়ে ইঞ্জিনিয়ার বন্ধু বিষয়টা খুব স্বাভাবিকভাবে নিলেন। ‘আরে, এতে আশ্চর্য হবার কী আছে? এসব এলাকায় এমন অনেক ঘটনা ঘটে যার কোন ব্যাখ্যা নেই। তুমি কি নেকড়েমানবের কথা শোনোনি? চোখ-কান খোলা রাখো, আরও অনেক কিছুই জানতে পারবে।’ এই বলে বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিলেন অস্টারস্টক। তিনি এই এলাকায় আছেন বেশ ক’বছর ধরে। অনেক কিছুই তাঁর নজরে পড়েছে। স্থানীয় আদিবাসীদের কথাও তাই হেসে উড়িয়ে দিতে পারেননি।
এরপর মাস দুয়েক তেমন কোন ঘটনা ঘটল না। তারপরই একদিন স্মিথ তাঁবু ফেললেন কুরগ্রাম নামের একটি গাঁয়ের ধারে। স্মিথের বাংলো থেকে চার মাইলটাক দূরের এই গ্রামটি পাহাড়ের লাগোয়া। আকারেও বেশ বড়। গ্রামের চারধারে ক্যাকটাসসহ নানা জাতের কাঁটাঝোপের বেড়া। এখানকার অনেক গ্রামেই এটা চোখে পড়ে। বাইরের লোককে দূরে সরিয়ে রাখাই লক্ষ্য। মোটামুটি হাজারখানেক লোক বাস করে গ্রামটিতে। অসভ্য অধিবাসীদের শরীরে কাপড়-চোপড়ের বড্ড অভাব।
স্মিথ এখানে এসেছেন ট্যাক্স আদায়ের জন্য। ট্যাক্স ধার্য করা হয়েছে মাথা প্রতি এক শিলিং। এই টাকাটা ব্যয় করা হবে রাস্তা তৈরিতে। শুরুতে চলল লোক গোনার কাজ। এর মধ্যেই একদিন একদল ফুলানি হাজির হলো। এই জাতের লোকেরা শ্বেতাঙ্গদের রীতিমত দেবতাজ্ঞান করে। শ্বেতাঙ্গদের প্রভাব বেশি যেসব এলাকায় সেসব এলাকায় থাকা তাদের পছন্দ। কাঁদতে কাঁদতে স্মিথের পায়ের কাছে ময়লা কম্বলের একটা পুঁটলি রেখে বলল, ‘হুজুর, আমাদের বড় বিপদ। রক্ষা করেন।’
এদিকটায় গরু চুরির ঘটনা ঘটে হরহামেশাই। আর ফুলানিরা দক্ষ পশু-পালক। বলা চলে গরু-মোষ পেলেই এরা জীবনধারণ করে। শুরুতে স্মিথের তাই মনে হলো গরু চুরির বিচার চাইতে এসেছে এরা। কিন্তু একটু পরেই পরিষ্কার হলো ব্যাপারটা আরও অনেক ভয়ানক। পুঁটলিটা খুলতেই চোখ আটকে গেল স্মিথের। আরে, এখানে তো পনেরো-ষোলো বছরের এক কিশোরের মৃতদেহ। গলায় গভীর একটা ক্ষত। দেখে মনে হয় কিছু একটা কামড়ে নিয়ে গেছে খানিকটা মাংস। এটা আর যা-ই হোক বর্শা বা অন্য কোন অস্ত্রের আঘাতে হয়নি। স্মিথের মনে হচ্ছে কোন বন্যপ্রাণীর আক্রমণে এই হাল হয়েছে হতভাগ্য ছেলেটার। তাঁর কাছে কাঁদতে কাঁদতে এই হত্যাকাণ্ডের বিচার চাইল সবাই। গোটা ঘটনাটা খুলে বলতে বললেন তাদের।
তারা যে কাহিনী বলল তা বেশ অদ্ভুত। দুই দিন আগের এক সন্ধ্যা। অন্য গরুগুলো ফিরে এলেও দুটি গরুর কোন হদিস নেই দেখে ওই ছেলেটাকে পাঠানো হলো ওগুলোর খোঁজে। এমনিতে সে বেশ সাহসী। কিন্তু একটু পরই ফিরে এল ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে। বলল একটা হায়েনা তাকে অনুসরণ করেছিল। শুধু তাই না কোনভাবেই তাড়াতে পারছিল না। ওটার মধ্যে অশুভ একটা কিছু আছে। গ্রামের লোকেরা ছেলেটার কথায় কান না দিয়ে ইচ্ছামত গালমন্দ করল তাকে। বলল, হায়েনা একা একা মানুষের ধারে-কাছে ভিড়তে ভয় পায়। এই ভীতু প্রাণীটার ভয়ে তার মত এক যুবক কিনা পালিয়ে এসেছে। অতএব ছেলেটা কী আর করবে, আবার গেল ওই গরুদুটির সন্ধানে। তবে চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছিল ভয়ে কাঠ হয়ে আছে।
ওই দিন ছিল অমাবস্যা। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। এর মধ্যে একটু পর পর হায়েনার ডাক শুনতে পেল ফুলানিরা। এদিকে ছেলেটার কোন খবর নেই। রাতে আর ফিরলই না সে। যেমন খোঁয়াড়ে এল না গরুগুলো।
ভোর হতেই কয়েকজন বেরিয়ে পড়ল ছেলেটা এবং গরুদুটির খোঁজে। একটু পরই ছেলেটার পায়ের ছাপ চোখে পড়ল দলটির। একপর্যায়ে পেল গরুর ছাপও। এখান থেকে জন্তুগুলোকে পেয়ে তাঁবুর দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে তরুণ। একটা জায়গায় বেশ বিশৃঙ্খলা হয়েছে মাটির চিহ্ন দেখে তা বোঝা গেল। এর একটু দূরে ঝোপের মধ্যে পাওয়া গেল ছেলেটার মৃতদেহ। গলার একটু মাংস খেয়ে নিয়েছে কিছু একটা। আশ্চর্য ঘটনা, সেখানে গরু বাদে আর কোন জন্তু- জানোয়ারের পদচিহ্ন নেই। তবে কয়েকটা জায়গায় গরুর পেছনে হায়েনার ছাপ দেখে বোঝা গেল গরুগুলোকে সে অনুসরণ করেছিল। স্মিথ বেশ চমকে উঠলেন। একাকী কোন হায়েনা একজন মানুষকে আক্রমণ করার কথা নয়। এদিকে গরুগুলোর পায়ের ছাপ দেখেও এমনটা মনে হচ্ছে না এরা ভয় পেয়ে দৌড়াদৌড়ি করেছে। ফুলানিরা তার কাছে কী চায় বুঝতে পারলেন না। কী কারণে এসেছে জানতে চাইলেন।.
ফুলানিদের দেখে মনে হলো সাদা মানুষের এই আচরণে খুব মর্মাহত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এক বুড়ো বলল, ‘হুজুর, তুমি যা ভাবছ তা নয়। ওটা মোটেই হায়েনা নয়। তাহলে গরুদুটোকে তাড়িয়ে বেড়ার ওপাশে রেখে আসত না। কুরগ্রামের ক্যাকটাসের বেড়া ঘেরা খোঁয়াড়টায় সেখানে এখন ঘাস খাচ্ছে আমাদের গরুদুটো। ওটা মোটেই হায়েনা ছিল না, ছিল মায়াবী এক মানুষ।
‘যদি কুরগ্রামের লোকেরা গরুদুটি চুরি করে থাকে তবে অবশ্যই ওদের শাস্তি হবে। কিন্তু ছেলেটার মৃত্যুর সঙ্গে ওদের কোন সম্পর্ক নেই। এটা হায়েনার কাজ। আমি গ্রামে পুলিস পাঠাব গরুর খোঁজে।’
ফুলানিদের মোটেই খুশি মনে হলো না স্মিথের বিচারে। তবে মুখে বেশি একটা প্রতিবাদ করল না। একজন বলে ফেলল, ‘হুজুর, তুমি কি আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবে? হায়েনাই যদি নাটের গুরু হবে তবে গরু ফেলে মানুষ শিকারে নামল কেন?’
স্মিথ কোন জবাব দিলেন না। সত্যি বলতে বিষয়টা তাঁর মনেও খচখচ করছিল। একসময় হতাশ ফুলানিরা চলে গেল।
তবে কথামত পরদিন কুরগ্রামে একজন কর্পোরালের নেতৃত্বে চার পুলিস পাঠালেন। হঠাৎ তাদের আগমনে হকচকিয়ে গেল কুরগ্রামের বাসিন্দারা। তারা গরুগুলো সরানোরও সময় পেল না। ধরা পড়ার পর বলল ওগুলো এমনি এমনি ক্যাকটাসের বেড়া ডিঙিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়েছে রাতের অন্ধকারে। কিন্তু গরুদুটোকে ওই বেড়া থেকে বের করে আনতে লাগল পাক্কা আধ ঘণ্টা। এতেই পরিষ্কার হয়ে গেল ওগুলো মোটেই একাকী ওখানে যায়নি। এদিকে স্মিথের কড়া নির্দেশ ছিল কর্পোরালের প্রতি চোরকে ধরে আনতে হবে। না পারলে হাতকড়া পড়বে গ্রামের সর্দারের হাতে। পুলিসরা গোটা গ্রাম তল্লাশি চালাল, কিন্তু কে চুরি করেছে বুঝতে পারল না। একপর্যায়ে হন্তদন্ত হয়ে সর্দার হাজির হলো। শুকনো শরীর, পাঁজরের হাড় গোনা যাবে। বয়স অন্তত তিন কুড়ি। সঙ্গে বেশ শক্তপোক্ত, কঠিন কয়েকজন যুবক। সব ঘটনা শুনে সর্দার যেন আকাশ থেকে পড়ল। বলল সে এসব বিষয়ে কিছু জানে না। কর্পোরালের মনে হলো আসলেই সে কিছু জানে না। তলে তলে কলকাঠি নাড়ছে অন্য কেউ। এই বুড়োকে শুধু শো হিসাবে সর্দার করে রাখা হয়েছে। কিন্তু কী আর করা! কর্পোরাল মুসা গোমবি সর্দারকে হাতকড়া পরিয়ে রওয়ানা হলো। যাওয়ার সময় হুমকি দিয়ে গেল চোরকে হাজির করা না হলে সর্দারকে থাকতে হবে কয়েদখানায়।
স্মিথের আস্তানায় আচ্ছাসে জেরা করা হলো সর্দারকে। একটা শব্দও বের করা গেল না তার মুখ থেকে। স্মিথের মনে হলো গোটা গ্রামে এই ঘটনা সম্পর্কে এই বুড়োই বুঝি বা সবচেয়ে কম জানে। সবচেয়ে অবাক ঘটনা, সর্দারকে ছাড়িয়ে নিতে কুরগ্রামের একজন লোকও এল না।
তবে এতেই দমে গেলেন না স্মিথ। নতুন বুদ্ধি বের করলেন। পুলিসের মারফত গ্রামবাসীদের জানালেন গরু যেহেতু তাদের গ্রামে পাওয়া গেছে তাই দণ্ড তাদের হবেই। শাস্তি হিসাবে দশটা ঘোড়া, একশো ছাগল এবং এবারের শস্যের একটা অংশ দিয়ে দিতে হবে। এবার সত্যি টনক নড়ল কুরগ্রামের লোকদের। সর্দারের জন্য তাদের মন একটুও না পুড়লেও জরিমানার কথা শুনে মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। কয়েকজনকে পাঠাল স্মিথের ক্যাম্পে। তারা এসে বেশ নরমভাবেই বলল এই চুরির পেছনে তাদের কোন ভূমিকা নেই। সাহেব কেন তাদের ওপর জুলুম করছেন! স্মিথ বললেন তাহলে তারা আসল চোরকে ধরিয়ে দিক। এবার তারা একজন আরেজনের মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। স্মিথ বুঝলেন একটা ঘাপলা আছে। চেপে ধরলেন। এবার স্বীকার করল সব কিছুই তারা জানে। কিন্তু বলার সাহস পাচ্ছিল না এতদিন। গ্রামের এক পাশে থাকে ‘জু জু’ নামের এক লোক। তাকে সবাই ভয় পায়। সে-ই সব কিছু করছে। দিনে মানুষ থাকলেও রাতে অসম্ভব ক্ষমতাধর এক হায়েনায় নিজেকে পরিণত করতে পারে এই মায়াবী। তার বিরুদ্ধে কিছু বললেই প্রাণ যাবে তাই এতদিন সাহস করেনি তারা। স্মিথ দেখলেন কুরগ্রামের লোক এবং ফুলানিদের কথা মিলে যাচ্ছে। মায়াবীকে ধরে আনার জন্য পুলিস পাঠালেন। তিন দিনের মধ্যে ধরে স্মিথের ক্যাম্পে নিয়ে আসা হলো তাকে।
লোকটাকে দেখে রীতিমত থ হয়ে গেলেন স্মিথ। এ কাকে দেখছেন! মনে হচ্ছে প্রাচীন যুগের কোন গুহামানব বুঝি বা এ যুগে হাজির হয়েছে। গায়ের রং কালো। তবে চোখগুলো নীলাভ। দ্যুতিহীন। আলো সহ্য করতে পারছিল না, পিট পিট করছিল। পেশীবহুল শরীর। গা লোমে ভর্তি বারবার চেষ্টা করছিল ছুটে পালাতে। মুখ দিয়ে ফেনা বের হচ্ছে। স্মিথের দেখেই মনে হলো এ হয়তো এসব কিছু করেনি। গ্রামের লোকেরা আধা মানুষ-আধা জন্তুটাকে বলির পাঁঠা বানাচ্ছে। তারপরও কয়েকদিন এখানে আটকে রাখার সিদ্ধান্ত নিলেন। এসময় স্মিথের বন্ধু অস্টারস্টকও উপস্থিত ছিলেন ক্যাম্পে। তিনিও অদ্ভুতদর্শন মানব-জন্তুটাকে দেখে চমকে উঠলেন। স্মিথ নানা ধরনের প্রশ্ন করলেন। একটারও উত্তর দিল না লোকটা। মুখ দিয়ে কেবল লালা গড়াচ্ছিল তার। অতএব কিছু খাবার দিয়ে আটকে রাখা হলো তাকে গোলাকার একটা মাটির ঘরে। খড়ের ছাদ, মাঝে শক্ত তালগাছের খুঁটি। দরজাটা তালাবদ্ধ। বাইরে অস্ত্র হাতে এক প্রহরী রাখা হলো। রাতে কয়েদখানায় উঁকি মেরে স্মিথ আর অস্টারস্টক দেখেন কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমাচ্ছে মানব-জন্তুটা। পানি খেলেও খাবার ছুঁয়েও দেখেনি। তার গা থেকে বের হওয়া বিকট গন্ধে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকাও কষ্টকর হয়ে পড়ল দু’জনের পক্ষে। তাড়াতাড়ি আবার তালা আটকে বের হয়ে এলেন দুই বন্ধু।
রাত তখন দশটা। খাওয়া শেষে বাইরে বসে আছেন দুই বন্ধু। ঘুটঘুটে অন্ধকার। হঠাৎ একটু দূরে একটা হায়েনার ডাক শোনা গেল। টানা, প্রলম্বিত একটা কণ্ঠ। এমন অদ্ভুত কণ্ঠে কোন হায়েনাকে এর আগে ডাকতে শোনেননি তাঁরা। একবার থামছে, তারপর আবার হচ্ছে। হঠাৎ কী একটা সন্দেহ করে দু’জনেই লণ্ঠন হাতে ছুটলেন কয়েদখানার দিকে। যা দেখলেন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এক প্রহরী এবং একজন পুলিস সদস্য মিলেও আটকাতে পারছে না আটক পশু কিংবা মানুষটাকে। খড়ের ছাদের নিচের বাঁশের বেড়াগুলোর ওপরে একটা গর্তমত করেছে সে। ওই ফাঁক দিয়ে বের হওয়ার চেষ্টা করছিল। এসময় শব্দ শুনে এগিয়ে আসে পুলিস আর প্রহরী। উপায়ান্তর না দেখে পুলিসটি বন্দুকের কুঁদো দিয়ে এত জোরে মারে লোকটার মাথায় সে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায় মাটিতে। কর্পোরাল এবার এগিয়ে এসে তালগাছের খুঁটির সঙ্গে হাতকড়া আটকে দিল বন্দির। সবাই ভাবল এবার আর বাছাধন পালাতে পারছে না।
পরের দিন রাত। প্রহরীর হঠাৎ একটু চোখ লেগে এল। তখনই তার মনে হলো পাশ দিয়ে কী একটা ছুটে গেল। লণ্ঠনের আলোয় দেখল দেয়ালে বিশাল এক গর্ত, ছাদটা নিচের দিকে নেমে এসেছে অনেকটা। সবাইকে সতর্ক করে দিতে শূন্যে গুলি ছুঁড়ল সে। তারপরই ক্যাম্পের প্রান্তে, প্রায় চারশো গজ দূরে পাহারায় থাকা প্রহরীটির গুলির শব্দও শুনতে পেল।
স্মিথ এবং অস্টারস্টক দৌড়ে গিয়ে দেখলেন বন্দি পালিয়েছে। সবচেয়ে ভয়াবহ ব্যাপার হলো তালগাছের খুঁটি দাঁত দিয়ে দুই টুকরো করে গিয়েছে সে। না হলে পালাতে পারত না। সেখানে পড়ে আছে অনেকটা লালা ও রক্ত। হাতকড়াটা গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে। গোটা কামরায় অসহ্য একটা গন্ধ। সাত দিন ধোয়া-মোছার পরে যায় ওই গন্ধ।
সবাই রীতিমত আতঙ্কিত হয়ে পড়ল ঘটনার আকস্মিকতায়। কয়েকজন পুলিস বেরিয়ে পড়ল। তারপরই তারা এসে একটা অদ্ভুত খবর দিল। ওপাশের প্রহরীর গুলিতে একটা হায়েনা মারা পড়েছে। কী আশ্চর্য! এত রাতে মানুষ ভর্তি ক্যাম্পে হায়েনা ঢোকা তো রীতিমত অস্বাভাবিক।
তবে কি ওই হায়েনা আর লোকটা একই ব্যক্তি? স্মিথ, বিশেষ করে তাঁর বন্ধু অস্টারস্টকেরও তা-ই মনে হলো। তাঁরা এগিয়ে গেলেন মৃত হায়েনাটার দিকে। হাঁ করা মুখটা পৈশাচিক। চোয়াল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত। প্রহরী বর্ণনা করল ঘটনা।
কয়েদখানা থেকে গুলির শব্দ শুনেই সতর্ক হয়ে যায় সে। বন্দুক বাগিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। হঠাৎ দেখে বিশাল একটা হায়েনা তাকে পাশ কাটিয়ে দৌড়চ্ছে আগুনের দিকে। আগুনে ঢুকেই পড়েছিল প্রায়। শরীরে আঁচ লাগতেই পিছু হটে। তখনই গুলি করে প্রহরী।
বিষয়টা নিয়ে অনেক ভেবেও কূলকিনারা করতে পারলেন না স্মিথ ও অস্টারস্টক। তবে শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন হয়তো হায়েনা আর ওই কয়েদী একই। কে না জানে আফ্রিকায় অনেক রহস্য লুকিয়ে আছে আজও। ফুলানি, কুরগ্রামের লোকেরা, এমনকী তাঁদের অভিজ্ঞতাও তো এই সাক্ষ্যই দিচ্ছে। তাছাড়া লোকটার চোখে একটু সমস্যা ছিল। তাই কি হায়েনাটা আগুনের ভেতরে ঢুকতে যায়?
কিলবার্ন স্টুডিয়োর ভুতুড়ে ঘটনা
ও’ডনেলের ভুতুড়ে বাড়ি আর জায়গা নিয়ে গবেষণা করার বাতিক ছিল। একদিন আলাপের সময় তাঁর বন্ধু জর্জ নিয়াল বললেন কোন বাড়ি ভুতুড়ে হওয়ার সঙ্গে এর পরিবেশ বা আবহাওয়ার যোগ আছে। যখন কোন বাড়ির পরিবেশ বা আবহাওয়া অস্বস্তিকর লাগবে তখন সেখান থেকে কেটে পড়া বা বাড়ি বদল করাই উত্তম। তাঁর মতে সমতল ও পাহাড়ি এলাকার থেকে নিচু এলাকায় এবং জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় খুন- খারাবি আর ভুতুড়ে ঘটনা বেশি ঘটে। যেমন ব্রিস্টল, বাথ এবং ক্লিভডনের মত এলাকাগুলোতে ভুতুড়ে বাড়ি ও জায়গার খবর বেশি পাওয়া যায়। কারণ এসব জায়গা নিচু। লণ্ডনের প্রসঙ্গ এলে এক্ষেত্রে সবার আগে আসবে কিলবার্নের নাম। এটাই লণ্ডনের সবচেয়ে ভুতুড়ে জায়গা। এখানকার পরিবেশটাই আসলে অতিপ্রাকৃত ঘটনার উপযোগী। তারপরই নিয়াল লিন্টন ওয়াইজম্যান নামের এক শিল্পীর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন।
সাদা-কালো ছবি আঁকতে ভালবাসতেন লিন্টন। মনের মত একটা স্টুডিয়ো খুঁজছিলেন অনেক দিন। শেষমেশ মোটামুটি পছন্দ হলো কিলবার্নের স্টেশনের ধারের একটি জায়গা। ওখানে আঁকাআঁকির সব সরঞ্জাম নিয়ে উঠে পড়তেও সময় লাগল না।
এক বিকালের ঘটনা। এক আত্মীয়ের একটা বইয়ের জ্যাকেটের কাজে বেশ খাটাখাটনির পর একটু বিরতি টানতে চাইলেন। চেয়ারটা ফায়ারপ্লেসের আগুনের সামনে নিয়ে একটা সিগার ধরালেন। এক চিত্রনায়িকার সঙ্গে লিণ্টনের বিয়ের কথা প্রায় পাকাপাকি। কিন্তু আর্থিক কিছু সমস্যার কারণে ওটা ঝুলে আছে। মেয়েটার কথা ভাবতে ভাবতে চেয়ারে হেলান দিয়ে পাইপ টানছেন। এসময় হঠাৎ তাঁর মনে হলো একমাত্র চাচার কথা। ভদ্রলোক চিরকুমার। তাঁর কাছে অনেক প্রত্যাশা লিণ্টনের। তাঁর মনে হলো চাচার খোঁজ-খবর পাওয়া যাচ্ছে না অনেক দিন। কয়েকবার চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু কোন উত্তর পাননি। তবে কি তিনি অসুস্থ? লিণ্টনের ওপর চাচার রাগ করার কোন কারণ নেই। আগামীকাল অবশ্যই আবার চিঠি লিখবেন তিনি। যদি তারপরও উত্তর না পান তবে সোজা টরকুয়েতে তাঁর বাড়িতে হাজির হয়ে চমকে দেবেন।
আসলে শিল্পী হিসাবে কদর থাকলেও এটা দিয়ে টাকা কামিয়ে বড়লোক হওয়ার ইচ্ছা তাঁর নেই। কিন্তু প্রেমিকার কথা চিন্তা করে এখন অর্থ-কড়ির কথা ভাবতে হচ্ছে তাঁকে। চিরকুমার বড়লোক চাচা যদি একটু এই তরুণ ভাতিজার কথা ভাবেন তবেই রক্ষা। আর চাচার কথা ভাবতে ভাবতে পাইপ টানতে টানতে, কখন চেয়ারে হেলান দেয়া অবস্থায় একটু তন্দ্ৰামত চলে এল বলতেই পারবেন না। এসময় একটা শব্দে তন্দ্রা টুটে গিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। স্টুডিয়োর দরজায় একটা করাঘাতের আওয়াজ। হতভাগাটা কে! বিরক্ত হয়ে ভাবলেন লিণ্টন। বাড়ির ঝি তো চলে গেছে আগেই। এখন তো সামনের বেলটা না বাজিয়ে কারও ভেতরে ঢুকতে পারার কথা নয়।
‘ভেতরে এসো,’ বললেন।
তারপরই বিস্মিত হয়ে আবিষ্কার করলেন দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করছে আধুনিক সাজসজ্জার এক তরুণী। জামাটা ঘন নীল, স্কার্ট খুব ছোট, কোটটা জাঁকালো, তাতে চমৎকার সব বোতাম শোভা পাচ্ছে। উঁচু হিলের চামড়ার জুতো পায়ে। মুখে মোহনীয় হাসি। হাসিটা ভালভাবে দেখতে পেলেন কারণ ওই মুহূর্তে হঠাৎ আগুনের শিখাটা বেশি করে জ্বলে উঠে তার মুখে পড়ে আলো। এমন এক চেহারা যেটা একজন এক পলকের জন্য দেখলেও সহজে ভুলবে না। নাকটা একটু বাঁকা, ভরাট স্তনদুটো যেন কাপড়ের শাসন মানতে চাইছে না, চোখের পাপড়ি ঘন। তবে লিন্টনকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করল তরুণীর চোখজোড়া। গভীর চোখদুটো নীল, এর মধ্যে এমন একটা প্রাণবন্ত ভাব আছে যা আগে কখনও দেখেননি তিনি। তবে দৃষ্টিতে কেমন একটা অস্থিরতা আছে। সব কিছু মিলিয়ে এই সৌন্দর্য তাঁকে রীতিমত টানতে লাগল। চোখজোড়ার মোহনীয় ক্ষমতায় এতটাই আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন যে, মুখের ভাষা হারিয়ে ফেললেন। শেষ পর্যন্ত কথা শুরু করল মেয়েটাই।
‘যাক, তোমাকে পেয়ে গেলাম। আর তুমি তো কাজও করছ না।’
কিছু বলার আগে আরেকবার তরুণীর দিকে তাকালেন। হাতের আঙুলে বেশ কয়েকটা আংটি শোভা পাচ্ছে। নখগুলো লম্বা, একটু বাঁকা, সেখানে আগুনের শিখা পড়ে ঝকমক করছে।
‘কিন্তু তুমি ঢুকলে কীভাবে?’ বিস্ময় কাটিয়ে জানতে চাইলেন লিণ্টন।
‘বেল বাজিয়ে,’ হেসে জবাব দিল তরুণী, ‘এটা খুব সহজ। অন্য কোন দিন বলব। এখন চলো আমার সঙ্গে। তোমাকে নিতে এসেছি।’
‘আমাকে নিতে!’ হতবাক লিণ্টন রীতিমত হাঁসফাঁস কণ্ঠে বললেন। ভালভাবে চোখ রগড়ে দেখলেন, না এটা স্বপ্ন নয়।
‘হ্যাঁ, ভুল শোনোনি। তোমাকে নিতে। দ্রুত হ্যাট আর কোট তুলে নাও। দোরগোড়ায় গাড়িটা অপেক্ষা করছে।’
রহস্যময় এই নারীর কথামত কাজ করতে শুরু করায় নিজেই অবাক হয়ে গেলেন লিণ্টন। কে সে? তাঁকেই বা কেন নিতে এসেছে? এটা জিজ্ঞেস করার বদলে তার মোহনীয় চোখের জাদুতে যেন রীতিমত সম্মোহিত হয়ে গিয়েছেন।
‘ঠিক আছে,’ বললেন লিন্টন। তারপর কোটটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘আমি আসছি। যাচ্ছি কোথায়?’
‘কেন, বাসায়,’ হেসে জবাব দিল নারীটি। ‘মনে হয় যেন তুমি কিছু জানো না। একজন মানুষ তোমাকে দেখতে পাগল হয়ে গিয়েছে। আমাকে দু’দণ্ড শান্তি দিচ্ছিল না। শেষমেশ প্রতিজ্ঞা করলাম গাড়ি নিয়ে এসে তোমাকে নিয়ে যাব। দুঃখজনক হলেও তোমার বাড়িতে ফোন নেই।’
‘আশা করি শীঘ্রিই আনতে পারব,’ কুণ্ঠার সঙ্গে বললেন লিণ্টন, ‘সত্যি বলতে, যখন ওটার খরচ পোষাতে পারব।’
‘পোষাতে পারবে!’ তার কথার প্রতিধ্বনি তুলল নারীমূর্তি, ‘তোমার চিত্রকর্মগুলোই যথেষ্ট। এগুলো দিয়েই টাকার পাহাড় বানাতে পারো। এখন জলদি চলো, তুমি বড্ড ধীর।’
বাড়ির দরজায় সত্যি একটা গাড়ি অপেক্ষা করছিল। তবে ভাড়া করা। সঙ্গীর সঙ্গে বিনা দ্বিধায় তাতে চেপে বসলেন লিন্টন।
গাড়ি চলতে শুরু করল। একটা রাস্তা ছেড়ে আরেকটা রাস্তায় ঢুকে পড়ছে ওটা। গ্যাসের ল্যাম্পের উজ্জ্বল আলোয় ভেতরটা আলোকিত। কিলবার্নের ভেতরই আছে তারা। সব কিছুই বাস্তব। একই সঙ্গে আবার কেমন জানি ধোঁয়াটে লাগছে তাঁর কাছে। তাঁর সুন্দরী সঙ্গী একটু পর পরই তার ছোট্ট, নরম হাত লিণ্টনের হাতের ওপর রাখছে। ভঙ্গিটা এমন যেন, বহু দিনের বন্ধুত্ব দু’জনের। আশ্চর্য হলেও লিন্টন উপভোগই করছেন। মনে হচ্ছে মেয়েটির তাঁকে নিতে আসা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু নয়। যদিও তিনি তার নামও জানেন না, এমনকী তাকে কখনও দেখেছেন এটাও মনে পড়ছে না। একপর্যায়ে বড় একটা স্কয়ারের এক কোনার একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়িটি। নিঃসন্দেহে সমাজের অভিজাত লোকেরাই বাস করেন এখানে।
গাড়ি থেকে লাফ দিয়ে নেমে তরুণী তাকে অনুসরণ করার ইশারা করল লিন্টনকে। কয়েকটা সিঁড়ি পেরিয়ে ওপরে উঠে চাবি দিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল, তারপর ভেতরে ঢুকল। লিন্টন তার সঙ্গে ভেতরে পা রাখতেই অদ্ভুত একটা নৈঃশব্দ্য চেপে ধরল তাঁকে। সব কিছু অদ্ভুত রকম সুনসান। মেয়েটা প্রতি কদম ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল বাড়িটায় তার হিলের শব্দের প্রতিধ্বনি হচ্ছে। তবে বাড়িটা চমৎকারভাবে সাজানো-গোছানো। কোথায় যেন একটা অসামঞ্জস্য আছে বুঝতে পারছেন না।
তাঁর চিন্তা বুঝতে পেরেই যেন সে বলে উঠল, ‘আশা করি তুমি মাফ করবে আমাকে। বাসাটা অতিরিক্ত চুপচাপ লাগছে। রাঁধুনির বোনের বিয়ের পার্টিতে যেতে চাকর- বাকরেরা এতটাই চেপে ধরল মানা করতে পারিনি।’
‘তাহলে বাড়িতে আমরা একা,’ যন্ত্রমানবের মত বললেন লিণ্টন।
একা!’ তার কথার পুনরাবৃত্তি করল নারী। নীল চোখে রহস্যময় হাসি। তারপর আবার বলতে শুরু করল, ‘যে কেউ তোমার চেহারার দিকে তাকালেই বুঝবে আমাকে ভয়ানক একটা কিছু ভেবে বসে আছ। কোন ধরনের স্ক্যাণ্ডাল কিংবা ব্ল্যাকমেইলের একটা আশঙ্কাও নিশ্চয়ই মনে দানা বাঁধছে। এখানে এসে একটু অপেক্ষা করো। এই ফাঁকে পোশাকটা বদলে নিচ্ছি। আজকে তার শরীরটা খুব একটা ভাল না। তাকে বিছানায় রেখে এসেছি।’
লিন্টনকে একটা কামরায় ঢুকিয়ে বাতি জ্বেলে ওপরের তলার দিকে দৌড়ে গেল তরুণী। সে চলে যাবার পর বেশ ক্লান্তি অনুভব করলেন লিন্টন। সারা দিনেই আঁকাআঁকি করেছেন। মৃদু আলো ছড়াতে থাকা গ্যাস বাতিটার সামনে একটা চেয়ারে গা ডুবিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করলেন। এই ফাঁকে গোটা বিষয়টি নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন। এটা ঠিক তিনি রোমাঞ্চ পছন্দ করেন, যেখানে বিপদ কিংবা রোমান্স আছে তা টানে তাঁকে। কিন্তু এর জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে তাঁকে। এখন তিনি খুব ক্লান্ত। তারপর আবার গোটা বিষয়টা কেমন খাপছাড়া, রহস্যময়। এই নারী কে? তাঁকে কেনই বা এ বাড়িতে নিয়ে এসেছে? সব কিছু এমন চুপচাপ কেন? তাঁর জন্য কে অপেক্ষা করে আছে? হঠাৎ মৃদু একটা শব্দ, অদ্ভুত একটা আওয়াজ, অনেকটা অপ্রত্যাশিত কোন ব্যথায় কেউ কেঁদে ওঠার মত, সচকিত করে তুলল তাঁকে। উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে তাকালেন। তবে শব্দটা আর শুনতে পেলেন না। আগের মতই নৈঃশব্দ্যের একটা চাদরে ঢাকা পড়ল গোটা বাড়ি। চেয়ারে ঠেস দিলেন আবারও। শেষ পর্যন্ত দীর্ঘ অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে দরজা খুলে ওই তরুণী সামনে এসে দাঁড়াল।
প্রেমিকার প্রতি বিশ্বস্ততায় কোন খাদ নেই লিণ্টনের। কিন্তু এই রহস্যময় নারীর প্রতি অপ্রতিরোধ্য একটা আকর্ষণকে দমন করা কষ্টকর হয়ে পড়ছে তাঁর জন্য। এই মুহূর্তে মাদাম ভারতেয়োল্লির ডিজাইন করা আধুনিক একটা পোশাক গায়ে চাপিয়েছে সে। তাকে এতটাই সুন্দর লাগছে যে দাঁড়িয়ে নির্লজ্জের মত তাকে দেখতে লাগলেন।
‘কী, লিণ্টন,’ হেসে সামনের আয়নার দিকে তাকিয়ে কোঁকড়ানো চুলগুলো একটু ঠিক করে নিয়ে বলল, ‘এভাবে তাকিয়ে আছ কেন? আমার মধ্যে কি কিছু দেখতে পাচ্ছ? ও, একটা কথা, কয়েক মিনিট আগে কি একটা শব্দ শুনতে পেয়েছ?’
‘আমার মনে হয়েছিল কেউ একজন ব্যথায় চিৎকার করে উঠেছিল। পরে মনে হলো, না, তন্দ্রায় বোধহয় স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলাম।’ জবাব দিলেন লিণ্টন।
‘না, তুমি সত্যি শুনেছ। ওটা আমি,’ নারীটি জানাল, ‘আমাদের পাজি বিড়ালটা আমাকে আঁচড়ে দিয়েছে, দেখো।’ বলে একটা হাত তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিল। ওটার পেছনে লাল, লম্বা একটা দাগ নজরে পড়ল লিণ্টনের। কেন যেন কেঁপে উঠলেন যুবক। যে কোন ধরনের রক্ত দেখলেই গা ছমছম করে ওঠে তাঁর।
‘কী ভয়ঙ্কর!’ বললেন লিণ্টন, ‘আশা করি ওটাকে কয়েক ঘা লাগিয়ে দিতে পেরেছ।
‘আরে, না। ধরতেই পারিনি। তবে একবার না একবার ঠিকই ধরা খাবে। সবসময় কাউকে না কাউকে আক্রমণ করবেই ওটা। কাল না পরশুই তো রাঁধুনিকে কামড়ে দিতে চেয়েছিল। এখন আর এসব কথা নয়। সাপারের সময় হয়েছে, চলো!’
হল পেরিয়ে ডাইনিঙে ঢুকল তারা। দু’জনের জন্য একটা টেবিল সাজানো হয়েছে সেখানে। এই সময়টার কথা কখনও ভুলবেন না লিণ্টন। কোঁকড়া চুলের ওই নীলনয়নার থেকে দৃষ্টি ফেরাতেই পারছিলেন না। যখন দৃষ্টি সরিয়েছেন তখনও নরম হাত, লম্বা আঙুল-নখ আর হাতেরই সাদা চামড়ার মাঝে সেই লাল আঁচড়টার দিকেই তাকিয়েছেন। মেয়েটার দিকে এতটাই মনোযোগ ছিল কী খেয়েছেন বলতে পারবেন না। নিজেকে অ্যালকোহলবিদ্বেষী বলে পরিচয় করিয়ে দিলেও আজ রাতে তরুণী যা-ই সামনে দিয়েছে গিলেছেন। একসময় শেষ হলো খাওয়া। তাঁর দিকে ঝুঁকে এল মেয়েটা। সুন্দর চোখজোড়ায় দুর্বোধ্য দৃষ্টি ফুটিয়ে তুলে বলল, ‘তোমার জন্য একটা সারপ্রাইজ লুকানো আছে আমার হাতায়। দেখতে চাও?’
‘অবশ্যই,’ জবাব দিলেন লিণ্টন। 1
‘তাহলে চলো,’ এই বলে চেয়ার থেকে উঠে পথ দেখাল। তবে তার পিছু নিয়ে এগুতে লিন্টনের বেশ বেগ পেতে হলো। মাত্রাতিরিক্ত ওয়াইনের প্রতিক্রিয়া। রীতিমত টলছেন তিনি। হল অতিক্রম করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে একটা সিঁড়ির সামনে থেমে দাঁড়িয়ে মেয়েটা বলল, ‘এখানে কি একটা মিনিট অপেক্ষা করতে পারবে? আমি গিয়ে দেখি সব ঠিকঠাক আছে কিনা।’ তারপর অদৃশ্য হলো মেয়েটা। আবার একা লিণ্টন। কৌতূহল নিয়ে চারপাশে তাকালেন। কেমন কু গাইছে মনে। এই মহিলা কি তবে এই বাড়িতে একাই থাকে? চাকর-বাকরদের ব্যাপারে বলা কথাটা কি সত্যি! আর অন্য একজনের কথা বলেছে সে-ই বা কোথায়? দেয়ালের একটা কুলুঙ্গিতে আবলুস কাঠের ফ্রেমে আটকানো বিশাল এক গ্র্যাণ্ডফাদার ক্লক। এক মনে ওটার দিকে তাকিয়ে ওটার টিক টিক শব্দ শুনতে লাগলেন। এসময়ই তরুণীটি এসে তাঁকে নিয়ে একটু দূরের আরেকটা কামরায় ঢুকল। তাঁর কাঁধে হাত রেখে ফিসফিস করে বলল, ‘আগুনের পাশের চেয়ারটায় তোমার জন্য একটা চমক অপেক্ষা করছে।’ কথা বলার সময় তার শ্বাসের গন্ধ তাকে রীতিমত আচ্ছন্ন করে ফেলল। মেয়েটা তাঁর আরও কাছ ঘেঁষে দাঁড়াল। এতটাই আপ্লুত হয়ে পড়লেন যে জড়িয়ে ধরে কোমলভাবে কয়েকটা চুমু দিলেন। কয়েক সেকেণ্ডে লিণ্টনের বাহুবন্ধনে আটকা থাকল মেয়েটা। তারপর হঠাৎ জোর করে ছাড়িয়ে নিল। তারপর হাসতে হাসতে তাঁর গায়ে টোকা দিয়ে কামরা থেকে বের হয়ে গেল, যাবার সময় দরজাটা ধাক্কা দিয়ে গেল।
‘চেয়ারের দিকে তাকাও,’ চেঁচিয়ে উঠল সে, ‘তাড়াতাড়ি! এত ধীর কেন তুমি?’ এসময়ই ক্লিক করে একটা শব্দ হলো। মনে হয় বাইরে থেকে দরজাটা আটকে দেয়া হয়েছে। এসময় আগুনটা হঠাৎ যেন ফুঁসে উঠল। এতে ধরা পড়ল সামনের চেয়ারটায় তাঁর দিকে পেছন ফিরে বসে আছে ফ্ল্যানেলের পোশাক পরা কেউ। লোকটার পাদুটো ছড়ানো। মাথাটা চেয়ারের পেছনে বিশ্রামরত। এতে পেছন থেকে মুখটা দেখতে পেলেন এখন লিণ্টন। তখনই মনে হলো অবয়বটার মধ্যে কোন একটা অস্বাভাবিকতা আছে। মুখটা সবুজ। চোখটা আধবোজা। মুখটা হাঁ করে আছে। ততক্ষণে কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন লিন্টন। চেয়ারটার সামনে গিয়ে আধশোয়া লোকটার দিকে তাকালেন সরাসরি। যা দেখলেন আতঙ্কে কয়েক কদম পিছিয়ে গেলেন। লোকটা আর কেউ নন-তাঁর চাচা। তাঁর অস্বাভাবিকভাবে শুয়ে থাকার কারণ পরিষ্কার। তিনি মারা গিয়েছেন। গলা কাটা। আ পরিষ্কারভাবে বললে ধারালো কিছু দিয়ে বারবার আঘাত কর। হয়েছে তাঁর গলায়। আবিষ্কারটা এতটাই ভয়ানক যে কিছু সময়ের জন্য চিন্তা করার শক্তিও হারিয়ে ফেললেন লিন্টন। জায়গাতেই দাঁড়িয়ে রইলেন কতক্ষণ। কেউ যেন বা পাজোড়া আঠা দিয়ে আটকে দিয়েছে মেঝের সঙ্গে। তারপর হঠাৎই কাজ করা শুরু করল তাঁর শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো। দরজার দিকে দৌড়ে গেলেন সাহায্যের, আশায়। ওটা আটকানো। দরজায় করাঘাত করতে লাগলেন জোরে। এসময় বাইরে থেকে শোনা গেল নারীকণ্ঠের অট্টহাসি।
‘ওহ, কত্ত বোকা তুমি। কেমন লাগল আমার সারপ্রাইজটা? চাচার টাকা চেয়েছিলে? কিন্তু হেরে গেলে। সব এখন আমার। বিয়ের সময়ই উইল করিয়ে সব আমার নামে লিখিয়ে নিয়েছি। আর তোমাকেও জেলে ঢুকতে হচ্ছে!’ হাসতে হাসতেই বলল তরুণী।
‘মানে? এই, শয়তান, তুমি কী বলতে চাচ্ছ?’ রাগে চেঁচিয়ে উঠলেন লিন্টন।
‘ফাঁদে আটকা পড়েছ তুমি। রেহাই পাওয়ার কোন সুযোগ নেই। দরজা তালা লাগিয়ে দিয়েছি। জানালাগুলোয় গ্রিল আছে। তোমার পোশাকের দিকে তাকালেই বুঝতে পারবে কেমন বুদ্ধি করে তোমাকে ফাঁসিয়েছি। যখন তুমি আমাকে চুমু খাচ্ছিলে এবং আমার পোশাক আর চুল থেকে সুগন্ধ নিচ্ছিলে, তখন তোমার চাচার কিছু রক্ত তোমার পোশাকে লাগিয়ে দিয়েছি। এখন হাসতে হাসতে মরে যাচ্ছি আমি। এক ঢিলে বুড়ো স্বামী এবং তার বেকুব ভাতিজার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি। এবার পুলিস ডাকতে চললাম।’
লিন্টন দরজার পাশেই টেলিফোনের কাছে যাওয়ার শব্দ শুনল তার। জেরাল্ড রোড পুলিস স্টেশনে ফোন দিয়ে সে বলছে, ‘আমি ইন্সপেক্টর, সার্জন কিংবা দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কাউকে চাই। তাড়াতাড়ি আসুন দয়া করে। ইটন স্কয়ারের নম্বর বাড়িতে একটা হত্যাকাণ্ড হয়েছে। আমার স্বামীকে তার ভাতিজা মেরে ফেলেছে। সৌভাগ্যক্রমে ঘটনাটা দেখে ফেলেছি আমি, বুদ্ধি করে আসামীকেও ওই কামরায়ই আটকে ফেলতে পেরেছি। খোদার দোহাই, শীঘ্রি আসুন।’
তারপরই তরুণীটি সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। হতাশ, বিপর্যস্ত লিন্টন মেঝের ওপর বসে পড়লেন। এভাবে কতক্ষণ কেটেছে বলতে পারবেন না। হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ কানে এল। একজন লোকের কর্কশ কণ্ঠ, তারপর ভারী কিছু পদশব্দ। পরমুহূর্তে সিঁড়ি বেয়ে তাদের ওঠার থপ থপ আওয়াজ। একমুহূর্ত পরই ল্যাণ্ডিঙে উঠে এল পদশব্দ। -তারপর চাবি দিয়ে দরজা খোলার আওয়াজ। দরজাটা যখন খোলা হচ্ছে, আশ্চর্য একটা অনুভূতি হলো লিণ্টনের, পরমুহূর্তেই জ্ঞান হারালেন তিনি।
যখন চোখ খুলে আশপাশে তাকালেন, বিস্মিত হয়ে দেখলেন, তাঁর স্টুডিয়োতে ফিরে এসেছেন। আগুনের সামনে ঠিক আগের অবস্থানেই, নিজেকে আবিষ্কার করলেন। পৈশাচিক ওই মহিলা হাজির হওয়ার ঠিক আগের অবস্থায় আছেন যেন। এসময়ই দরজায় করাঘাতের আওয়াজ। তবে স্টুডিয়োর নয়, ঘরের প্রধান দরজায়। বারবার শব্দটা হতেই লাগল। সিঁড়ি বেয়ে নেমে দরজা খুলতেই একটা ছেলের দেখা পেলেন। হাতে একটা নোট। এখন পুরো সচকিত লিন্টন পড়তে শুরু করলেন, ‘প্রিয় ভাতিজা, অনেক দিন হলো আমার কোন খবর না পেয়ে তুমি নিশ্চয়ই চিন্তিত। তোমাকে না জানিয়ে একটা কাণ্ড করে ফেলেছি আমি, বিয়ে করেছি। আমার স্ত্রী চমৎকার এক আমেরিকান তরুণী। আশ্চর্য বিষয়, এখন যেখানে তুমি থাক একসময় সেখানেই থাকত সে। তোমাকে দেখতে অধীর হয়ে আছে ও। আজ রাত আটটায় কি আমাদের সঙ্গে ডিনার করবে? রাগ কোরো না। তোমার চাচা রবার্ট।
‘ও, একটা কথা, আমার বাসা বদলেছি। আমার পুরনো বাড়িটা ছিল চিরকুমার একজনের উপযুক্ত। কিন্তু একজন বিবাহিত লোকের জন্য না। আমার নতুন ঠিকানা…
ঠিকানাটার দিকে তাকালেন লিন্টন। ইটন স্কয়ারের একটা বাড়ির নম্বর। বিপদের একটা আশঙ্কায় দৌড়ে ওপরে উঠে কাপড় বদলালেন। এবং যথাসময়েই চাচার বাসায় পৌঁছলেন।
ভেতরে ঢুকতেই একটা ধাক্কা খেলেন। ঘণ্টাখানেক আগে ভয়াবহ দুঃস্বপ্নে যে বাড়িটায় এসেছিলেন সেটার সঙ্গে এর দারুণ মিল। ওই ঘড়িটা, ওটার টিকটিক আওয়াজ শুনতে পেলেন। বাড়িটাও কেমন সুনসান। ‘ড্রইং রুমে প্রবেশ করতেই তাঁর চাচা একটু লজ্জিত ভঙ্গিতে স্বাগত জানালেন। তাঁর গলার দিকে চোখ চলে গেল লিণ্টনের। সেখানে কোন ক্ষত নেই। কীভাবে প্রিয়তমার দেখা পেয়েছেন চাচা সে বর্ণনা দিচ্ছিলেন, এমন সময় ভেতরে ঢুকল এক নারী।
‘লিণ্টন, এই আমার স্ত্রী।’ বলে উঠলেন চাচা। তবে তার কোন প্রয়োজন ছিল না। এ তো নীলনয়না সেই নারী। তাঁর স্বপ্নে যে হাজির হয়েছিল।
‘এই হচ্ছে গল্প,’ সমাপ্তি টানলেন নিয়াল, ‘লিন্টনের মুখ থেকে শুনেছি। ওটা কি স্বপ্ন নাকি অন্য কিছু এর কোন উত্তর সে পায়নি। তার কি এখন চাচাকে সাবধান করে দেয়া উচিত? কী বলো, ও’ডনেল?’
‘জটিল এক প্রশ্ন। ভেবে দেখতে হবে,’ বললেন ও’ডনেল।
***