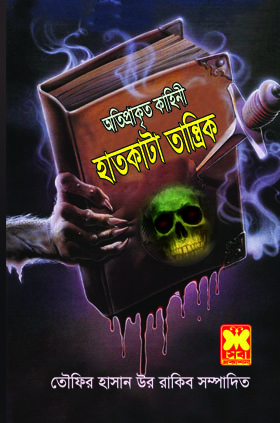- বইয়ের নামঃ হাতকাটা তান্ত্রিক
- লেখকের নামঃ তৌফির হাসান উর রাকিব
- সিরিজঃ সেবা হরর সিরিজ
- প্রকাশনাঃ সেবা প্রকাশনী বই
- বিভাগসমূহঃ ভূতের গল্প
হাতকাটা তান্ত্রিক
হাতকাটা তান্ত্রিক – মুহম্মদ আলমগীর তৈমূর
এক
আমার বি. এ. ফাইনাল পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল ১৯৭১ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি দেশ জুড়ে চলছে যুদ্ধের ডামাডোল। সব কিছু স্বাভাবিক আছে এইটে দেখানোর জন্যে পাকিস্তান আর্মি এই ধুন্ধুমারের ভেতরই টিচারদের দিয়ে একরকম জোর করেই ক্লাস নেয়াচ্ছে। সেনাবাহিনীর লোক লাগিয়ে গার্ড দেয়াচ্ছে পরীক্ষার হল। গুজব রটল পরীক্ষার হলে গার্ড দেয়া সেপাইরা আসলে একদম মাথামোটা। হলে দেদারসে নকল করলেও ব্যাপারটা একেবারেই ধরতে পারে না তারা। তাদের সাথে যেসব নরমাল টিচাররা থাকে, তারা এসব দেখেও, ভান করে না দেখার! কার গোহালে কে দেয় ধুয়ো!
নকল করে পাশ করার এমন স্বর্ণযুগ অতীতে আর কখনও আসেনি। বছর-বছর ফেল-করা ছাত্র যারা পরীক্ষার সময় এগিয়ে এলে দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর মত নির্জীব হয়ে যেত, নকল করে পাশ করার উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটতে লাগল তারাও। উত্তেজনার কারণ অবশ্য আরও একটা ছিল। সেই সময় বি. এ. পাশ ছেলের বিয়ে হত ভাল ঘরের সুন্দরী মেয়েদের সাথে। কোনওমতে একবার বি. এ. পাশ করতে পারলেই হয়-সুন্দরী বউ, লাগোয়া বাথরুমসহ ছোট্ট দুরুমের বাসা, ফিলিপ্স রেডিয়ো, শনি-রবি ঘোরাঘুরি, এন্তার খাওয়া হাতকাটা তান্ত্রিক দাওয়া!
যা হোক, লুঙ্গিতে মালকোঁচা মেরে আমিও রেডি হতে লাগলাম পরীক্ষার জন্যে। যেসব প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করতে পারিনি, সেগুলোকে চিরকুটের মত কাগজে লিখে নকলের চোথা বানালাম। চোথা হলো চিকন করে কাটা কাগজের ইয়া লম্বা ফালি। অনেকে ফালি কেটে ছোট-ছোট টুকরো করে। তবে এতে সমস্যা আছে। কোনটা আগে আর কোনটা পরে বোঝার জন্যে চিরকুটের গায়ে সিরিয়াল নাম্বার দিতে হয়। না হয়, একটার পর একটা সাজিয়ে সুই সুতো দিয়ে সেলাই করতে হয়। তারপরেও টানাহেঁচড়ায় এলোমেলো হওয়ার ভয় থাকে। যদি হয়, তা হলে সিরিয়ালি টুকরো সাজাতেই পেরিয়ে যাবে পরীক্ষার অর্ধেক টাইম! চোথা তৈরি করতে গিয়ে দেখলাম পড়ে পাশ করার থেকে নকল করে পাশ করা ঢের বেশি কঠিন! প্রচুর লেখালেখি করতে হয় একাজে। অতিরিক্ত পরিশ্রমী ছাত্রেরাই কেবল নকলবাজ হতে পারে। সাধারণ শিক্ষার্থীরা এত খাটনি খাটতেই পারবে না!
জুলাই মাসের গোড়ার দিকে বন্যার জলে ডুবে গেল সারা দেশ। রাস্তায় যদি মাজা সমান জল হয়, তো পরীক্ষার হলে হাঁটু সমান। জলকে যমের মত ভয় পেত খান সেনারা। ছাউনি থেকে বেরই হলো না তারা। লাটে উঠল পরীক্ষা। কী আর করা, এদিক-সেদিক ঘুরতে লাগলাম আমি। তবে সেখানেও সমস্যা আছে। যখন-তখন খান সেনারা রাস্তায় ধরে জিজ্ঞেস করে, তোম্ মুক্তি হ্যায়? আরে, বাবা, আমি যদি মুক্তি হইও, তবুও সেইটে তোকে বলব নাকি রে, গর্দভ! কলেজের আইডি কার্ড শো করার পরেই কেবল ছাড়া পেয়েছি। সেই আইডির মেয়াদও পার হয়ে গেছে এখন। দেখলাম, আমার অনেক বন্ধু-বান্ধব ঘুরতে যাচ্ছে ইণ্ডিয়ায়। বর্ডার নাকি ওপেন করে দেয়া হয়েছে। ওখানে গিয়ে পৌঁছতে যতক্ষণ, ব্যস তারপরেই ওপার। তবে হ্যাঁ, হেঁটে যেতে হবে। গাড়ি-ঘোড়া নেই। আমার বাড়ি থেকে বর্ডারের দূরত্ব পঞ্চান্ন কি. মি.! ঐকিক নিয়মে অঙ্ক কষে দেখলাম, হাঁটার গতিবেগ ঘণ্টায় তিন কি. মি. হলে পঞ্চান্ন কি, মি. পাড়ি দিতে লাগবে আঠারো পূর্ণ একের তিন ঘণ্টা! বুঝলাম ওপারে বেড়াতে যাওয়া সহজ নয় মোটেও।
ইণ্ডিয়ায় যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না, তবুও যেতে অনেকটা বাধ্যই হলাম। অগাস্টের শুরুতেই দেখা দিল মঙ্গা। পিস কমিটির লোকেরা নৌকোয় চড়ে ছোট-ছোট পলিথিন ব্যাগে ভীম মোটা আতপ চাল আর মসুরির ডাল দিয়ে যেতে লাগল। দিলে কী হবে! দুদিনেই শেষ হয়ে যায় রিলিপ। ওদিকে পরবর্তী রিলিপ আসতে আরও সাত দিন বাকি! বলতে গেলে, ইউসুফ নবীর ভাইদের মত খাওয়ার অভাবেই দেশান্তরী হতে হলো আমাকে।
পাকিস্তান ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ভেঙে সাত টাকা বারো আনা পেলাম। আগের বছর উল্টোরথের মেলা থেকে মাটির ওই ব্যাঙ্কটা কিনেছিলাম। খুচরো পয়সাগুলো আবুল মিয়ার বিড়ি সিগারেটের দোকানে নিয়ে নোট বানালাম। এরপর সেরখানেক চিড়ে আর পোয়াটাক আখের গুড় কিনে রওনা হলাম। পরনে রুহিতপুরি লুঙ্গি, হাওয়াই শার্ট। পায়ে স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল। হেঁটে সাঁতরে পেরিয়ে গেলাম জলে ডুবে থাকা ফসলের মাঠ, কলাগাছে ঘেরা গ্রাম, কালো ক্যানেস্তারা দিয়ে। বানানো টঙ-দোকানঅলা বাজার। এভাবেই চলল পুরো একদিন। পরদিন সন্ধের সময় টনটনে পা আর বিধ্বস্ত শরীর নিয়ে পৌঁছলাম বর্ডার থেকে পাঁচ কিলো দূরে মালিথা পাড়ায়। নদীর ধারে ইয়া বড় বটগাছের তলায় চা-মুড়ি খেতে-খেতে শুনলাম: বড় মালিথার বাড়িতে রাতে অতিথি থাকতে দেয়।
আঠারো বিঘে জমির ওপর বিশাল এক বাড়ি। পাকা কুঠি, টিনের চালা, খড়ের ছাউনি-স্থাপত্যকলার সব নিদর্শনই আছে এখানে। বড় মালিথার লম্বা দাড়ি, সিংহের থাবার মত প্রকাণ্ড হাতের পাঞ্জা। তবে কনুই থেকে নেই একটি হাত। পাথর কুঁদে বানানো ঝামা কালো চেহারা যেন। ইমাম সাহেবদের চেকচেক উড়ুনিতে ঘাড়-মাথা ঢাকা। কথা-বার্তা শুনে মনে হলো অসম্ভব ভদ্র আর জ্ঞানী এই লোক। বান-ডাকা নদী থেকে খ্যাপলা জালে ধরা ডিমঅলা রায়েক মাছের ঝোল দিয়ে গরম ভাত খেলাম। এত স্বাদের তরকারি জীবনেও খাইনি। পরদিন সকালে নুন-ঝাল আর চাকচাক করে কাটা বেগুনভাজি দিয়ে খিচুড়ি খেয়ে আরও জনা আষ্টেক শরণার্থীর সাথে রওনা হলাম বর্ডারের উদ্দেশে। তবে তার আগে বিদায় নিতে গেলাম বড় মালিথার কাছে। ভদ্রলোক বললেন, ঘরে ফেরার পথে আপনার সাথে আবার দেখা হয়েও যেতে পারে। কে জানে! ভাল থাকেন।
নদীর ধার ঘেঁষে শুকনো রাস্তা দিয়ে হাঁটলে বামে নদী, ডানে বাঁশ-বাগান অথবা আম্রকানন। এন্তার লাশ পড়ে আছে। বাগানগুলোর ভেতর। কুকুর-শেয়ালে টানাটানি করছে। ওগুলো। ভ্রূক্ষেপও করছে না কেউ। রণাঙ্গনে বাঁচা-মরা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা! নদীর জলে লাশ হয়তো ভাসিয়ে দেয়া যেত। তবে তাতে বিনষ্ট হতে পারে পরিবেশ। এখানকার লোকেদের খাওয়া-রান্না-স্নান সবই ওই নদীর জলে!
আমাদের সাথের এক পরিবার বুড়ো ঠানমাকে ডুলির ভেতর বসিয়ে বাঁশের বাঁকে করে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। পালা করে একজন করে বইছে তাকে। বাঁকের সামনের ডুলিতে বাচ্চা দুটো ছেলেমেয়ে, পেছনেরটায় ঠানমা।
অর্ধেক রাস্তা পার হওয়ার পর বাজার মতন একটা জায়গায় জিরোতে বসলাম সবাই। ঠানমাকে বয়ে আনা লোকগুলোর লুতাভুতা অবস্থা। ঢকঢক করে জল খেয়ে ফোঁসফোঁস করে দম ছাড়তে লাগল তারা। শুনতে পেলাম ফিসফিস করে একজন আরেকজনকে বলছে, ওই বুড়ি মরে না কেন? আর তো পারি না, বাপু! চল, এক কাজ করি, বুড়িকে এখানেই ফেলে সটকে পড়ি আমরা!
এ কী বলছ, দাদা? মাকে রাস্তায় ফেলে যাবে? ভগবানে
সইবে না! বলল অন্যজন। এ প্রথমজন এইবার বলল, তা হলে এক কাজ কর। এখন থেকে তুই ওকে বয়ে নিয়ে যা। আমি আর পারব না, এই বলে দিলাম। তোর বউদিকেও বলেছি গতরাতে। তার মত আছে এ কাজে।
ঠিক আছে। বলছ যখন, দেখ কী করবে? উত্তর দিল দ্বিতীয়জন। এক সেকেণ্ডও লাগল না মত পাল্টাতে। ঠেলার নাম বাবাজি!
এরপর ঠানমার ডুলিটার দিকে এগিয়ে গেল প্রথমজন। গলায় মধু ঢেলে বলল, মা, এইখানে একটু বসো তুমি। দিলু-মিলুর মাকে নিয়ে পাড়ার ভেতর বাথরুম করাতে যেতে হবে। আমরা এই যাব আর আসব। ঠিক আছে? এই রে, দিলু-মিলু, তোরা না বাথরুম করবি বলছিলি? চল, যাই এখন। গাঁয়ের ভেতর থেকে বাহ্যি ফিরে আসি। তোর মাকেও বল। একসঙ্গেই যাব সবাই।
ছেলে যেমন বুনো ওল, মা-ও তেমনি বাঘা তেঁতুল। ঠানমা বলল, ওরে, বিশু। আমারও যে পেছন ফিরতে হবে। অনেকক্ষণ চেপে রেখেছি, এই বেলা না গেলেই নয়। রাস্তায় চলার সময় যখন-তখন তো আর তোদের থামতে বলতে পারি না। জানিস তো, যাত্রাপথে ঘনঘন থামা বিরাট কুলক্ষণ!
ঠানমার বুদ্ধির তারিফ করতেই হবে। এইখানে ফেলে গেলে নিশ্চিত মৃত্যু হত তার। অথচ এখান থেকে বর্ডারের দূরত্ব মাত্র দুই কি. মি.! গোয়ালন্দের ওপারে মানিকগঞ্জ থেকে প্রথমে নৌকোয় চড়ে তারপর হেঁটে এসেছে পরিবারটা। পাড়ি দিয়েছে সোয়া শ কিলো পথ। অথচ আর মাত্র দুকিলো যখন বাকি, ধৈর্য হারিয়ে ফেলল ঠিক তখনই! মানুষের স্বভাবই তাই। বছর ভরে কষ্ট করে শেষের দিকে হাল ছেড়ে দেয়া। অথচ ওটাই আসল পরীক্ষা!
প্রাগপুর বর্ডার পার হয়ে ইণ্ডিয়ার শিকারপুরে এলাম আমরা। সেখান থেকে বাসে চড়ে কোলকাতা শহরে। জীবনে এই প্রথম দেখলাম ট্রামগাড়ি। গুটুর-গুটুর করে এগিয়ে যাচ্ছে কচ্ছপের মত। হ্যাঁণ্ডেল ধরে অনবরত ওঠা-নামা করছে। যাত্রী। কোলকাতায় তো এলাম, কিন্তু উঠব কোথায়? এখানে সেখানে থিকথিক করছে জয় বাংলা-র লোক, অর্থাৎ বাংলাদেশি শরণার্থী। সারাদিন রাস্তায়-রাস্তায় ঘোরাঘুরি করা ছাড়া অন্য কোনও কাজ নেই এদের। বুকে ব্যাজ লাগানো ভলেন্টিয়ার আছে কিছু। ওদেরকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিলাম শরণার্থী ক্যাম্পটা কোথায়।
বিশাল এক খোলা মাঠের ভেতর শরণার্থী ক্যাম্প। তাঁবুর পর তাঁবু, অস্থায়ী ছাউনি। ঝিরঝিরে বৃষ্টি। থিকথিকে জল কাদায় ডুবে যাচ্ছে পায়ের গোড়ালি। শৌচাগার বলে কিছু নেই এখানে। যে যেখানে পারে, সেরে নিচ্ছে কাজ। মল মূত্রের দুর্গন্ধে আকাশ-বাতাস সয়লাব। শিশুদের ঊ্যা-ঊ্যা, মায়েদের খিস্তি-খেউড়, বুড়ো-বুড়ির ভগবান তুলে নিয়ে যায় না কেন! লক্ষ-লক্ষ জনতা-আমাশা, কলেরা, টাইফয়েড। এ এক জীবন্ত নরক! মনে পড়ল বড় মালিথার কথা, ইণ্ডিয়ায় যাবেন, বাবা? কিন্তু, ওখানে তো ভাল থাকতে পারবেন না। আমাদের কোনও জায়গা নেই সেখানে!
মাথা গুঁজবার মত কোনও জায়গাই পেলাম না শিবিরে। তিন বেলা লপসি খেতে লাগলাম। ডাল, মোটা চাল, আর সস্তা সজি দিয়ে এক ধরনের জলো খিচুড়িকে এরা বলে লপসি। সারাদিন রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরি আর তিন বেলা লপসি খাই। রাতে শুই মন্দির চাতালে। ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং। হট্ট মন্দির! বুঝলাম, এভাবে বাঁচতে পারব না। ভাল পরিবেশ চাই আমার। থাকতে হবে স্নান-আহারের সুবন্দোবস্ত আর ভাল শৌচাগার!
তিন দিনের দিন সকালের লপসি খেয়ে শিবির থেকে বেরুতে যাব, ঠিক সেই সময় দেখলাম কীসের যেন জটলা। কী? নাহ্, মুক্তিফৌজের লোক রিক্রুট হচ্ছে। খোঁজ-খবর নিয়ে জানলাম মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিলে ট্রেনিং ক্যাম্পে খাওয়া-থাকার সুবন্দোবস্ত আছে। এই তো চাই! মনে-মনে বললাম আমি। আগে জান তো বাঁচাই। যুদ্ধ পরে দেখা যাবে!
দুই
শেয়ালদা থেকে লোকাল ট্রেনে করে আমাদের নিয়ে আসা হলো বিহারের শাশারাম জেলায়। এরপর আর্মি ট্রাকে তিন ঘন্টা জার্নি করে এলাম এক বাজপড়া এলাকায়। পথে রোহতাস নামে ছোট্ট একটা শহরে ট্রাক থামিয়ে চা-বিস্কুট খেতে দিয়েছিল। আশপাশে বিশ কিলোর ভেতর কোনও জনবসতি নেই। উষর মরুভূমির মত পরিবেশ। বৃষ্টি-বাদলের চিহ্নও নেই কোথাও। তাপমাত্রা বেয়াল্লিশের নিচে কখনও নামেই না। দুই সারি পাহাড়ের মাঝখানে খোলা বাটির মত জায়গায় ট্রেনিং ক্যাম্প। মূল রাস্তা থেকে র্যাম্পের মত উঠে গেছে এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে পথ। তারপর ডানে মোড় নিয়ে আবারও ঢালের মত নেমে গেছে বাটির মত বৃত্তাকার উপত্যকায়। ঢালের গোড়াতেই ছোট্ট চেকপোস্ট। পরিষ্কার। বুঝতে পারলাম, আগে থেকে জানা না থাকলে ভীষণ কঠিন এই জায়গা খুঁজে বার করা! পাহাড় ঘেষে লম্বা ব্যারাক। ব্যারাকের একপাশে খাওয়ার মেস, অন্যপাশে হাম্মাম খানা।
প্রতি এক শজন মুক্তিযোদ্ধার জন্যে আটজন ট্রেনার। আগে থেকেই পঁচাত্তরজন ছিল ওখানে। আমাদের দলে পঁচিশজন-সব মিলে এক শ। বারোজনের এক-একটা গ্রুপ। তৈরি করে শুরু হলো ট্রেনিং। আমাদের গ্রুপের জি. আই. বা ট্রেনারের নাম সতীশ লাল রায়, সংক্ষেপে এস, এল. আর.। ঝটা গোঁফ, কদমফুল চুল। গায়ে হাতাঅলা মুগায় কাটা গেঞ্জি আর ঢোলা হাফ প্যান্ট। পায়ে পেছন-কাটা পামশু। এই এস, এল, আর, আমাদের শেখাল কীভাবে গ্রেনেড ছুঁড়তে হয়, চালাতে হয় এস, এল, আর. (সেমি অটোমেটিক লংরেঞ্জ রাইফেল)। ট্রেনিং দিতে গিয়ে এস, এল, আর. বললেন, এস. এল. আর.-এ ফায়ার ওপেন করলে প্রথম ম্যাগাজিন কোনওরকম ঝামেলা ছাড়াই শেষ হয়। তবে দ্বিতীয় কিম্বা তৃতীয়টার বেলায় লাল টকটকে হয়ে ওঠে ব্যারেল, আগুনের মত গরম হয়ে যায় এস, এল, আর.। তখন ওটাকে হাতে ধরাই যায় না। এইম করে দুশমনকে গুলি করা তো অনেক পরের ব্যাপার! এই সমস্যার সমাধান হলো জল দিয়ে ব্যারেল ভেজানো। রণাঙ্গনে জল আর পাওয়া যাবে কোথায়! অ্যামবুশ ফেলে জল আনতে গেলে নিজের জীবন তো যাবেই, সেই সাথে যাবে সঙ্গীরও। চাই তাৎক্ষণিক সরল সমাধান, আর সেইটে হলো লুঙ্গির কাছা খুলে ব্যারেলের ওপর পেশাব করা! বন্ধুরা, অপারেশনে যাওয়ার আগে যত বেশি পারেন জল খেয়ে নেবেন!
.
সন্ধের পর-পরই সেরে ফেলা হত খাওয়া-দাওয়া। রাত দশটার ভেতর হ্যারিকেন নিভিয়ে শুয়ে পড়া বাধ্যতামূলক। খাওয়ার পর এই রাত দশটা পর্যন্ত কোনও কাজই নেই। সব থেকে কষ্টের ছিল রোববারের দিনটা। রোববার সাপ্তাহিক ছুটি, ট্রেনিং-ফ্রেনিং সব বন্ধ। সকালবেলা কাপড়-চোপড় কেচে শুকোতে দিয়ে সারাদিন বিছানায় বসে থাকা! রুমমেটরা চাষাভুষো ধরনের, এদের সাথে কথা বলে কোনও আরামই পাই না। ম্যাট্রিক পাশ চ্যাংড়া মতন একটা ছেলে আছে। বাবার ওপর অভিমান করে নাম লিখিয়েছে মুক্তিফৌজে। এখন বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্যে কেঁদে বুক ভাসাচ্ছে। রাতদিন তার মুখে শুধু বাড়ির কথা। মুখে গুটিবসন্তের দাগঅলা তালপাতার সেপাইয়ের মতন ডিগডিগে আরেকজন আছে। বছর ত্রিশেক বয়স। এ নাকি ডাকাতি করত। কাকে কোথায় জবাই করে পুঁতে রেখেছে, মুখে শুধু সেই কাহিনী। যতজনকে এ খুন করেছে, সেই হিসেব করলে অর্ধেক গাঁ, বিহারের আঞ্চলিক ভাষায়, উজড়া হয়ে যাওয়ার কথা! চূড়ান্ত মিথ্যুক এই গুটিবসন্ত। আমার ধারণা, এ ব্যাটা আসলে ছিঁচকে চোর। কাউকে খুন করার মুরোদ এর কোনওকালেই ছিল না। গাঁয়ের লোকের মারের হাত থেকে বাঁচার জন্যে নাম লিখিয়েছে মুক্তিবাহিনীতে! তিন নম্বর রুমমেট এক ফুলবাবু। দেশ যাচ্ছে রসাতলে, মরব কি বাঁচব তার নেই ঠিক। ওদিকে এর ব্যাগের ভেতর স্নো আর পাউডার! সন্ধের পর ক্লিন শেভ করে স্নো-পাউডার মাখে। তারপর হাতলঅলা ছোট আয়নায় কিছুক্ষণ পর-পর মুখ দেখে। গুনগুন করে গানও গায়: আমার গলার হার খুলে দে এ-এ-এ, ও, ললিতে…
জেনেছি এ যাত্রাদলে বেহুলা সেজে মেয়েদের পার্ট করত। রাজাকারেরা তাকে নাকি ধর্ষণ করতে চেয়েছিল! মুক্তিযুদ্ধ করে এর প্রতিশোধ নিতে চায়!
তিন
বিশ দিনের মাথায় হাঁফিয়ে উঠলাম আমি। কোথাও না কোথাও একটু বেড়িয়ে না এলে আর চলছে না। কিন্তু যাব কোথায়? এই এলাকার কিছু চিনি না। চিনলেও বা কী? ক্যাম্প ছেড়ে যাওয়ার কোনও হুকুম নেই। তারপরেও অনুরোধ করেছিলাম এস, এল, আর.-কে। কিন্তু লাভ হয়নি কিছু। এরই ভেতর একদিন এক ঘটনা ঘটল। রামেশ্বর কাউর নামে এক ব্রিগেডিয়ার এল ক্যাম্প দেখতে। খুব বিখ্যাত লোক, সেনাবাহিনীতে নাকি বিরাট নাম-ডাক। অনেক পরে জেনেছি, ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র-এর প্রধান ছিল কাউর! কয়েকজনকে ডেকে এটা ওটা জানতে চাইল ব্রিগেডিয়ার সাহেব। এই কয়েকজনের ভেতর পড়ে গেলাম আমিও। সম্ভবত লেখাপড়া জানা থাকার কারণেই ডাকা হলো আমাকে। দোভাষীর মাধ্যমে হিন্দিতে কথা বলছিলেন কাউর সাহেব। আমি তার সাথে সরাসরি ইংরেজিতে কথা বললাম। জানালাম, খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা মোটামুটি ভাল হলেও আমাদের কোনও প্যান্ট দেয়া হয়নি। বুটের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে থাকি, ট্রেনিং করতে হয় মালকোঁচা মেরে! লুঙ্গি-গেঞ্জি-কে ইংরেজিতে লুঙ্গি-গেঞ্জি বলায় হাসতে লাগল কাউর। বলল, উই উইল সি টু ইট। ইউ ক্যান গো নাও।
ততক্ষণে হালকা হয়েছে পরিবেশ। সাহস বেড়ে গেছে আমার। বললাম, স্যর, এক জায়গায় থাকতে-থাকতে হাঁপিয়ে উঠেছি আমি। একদিনের জন্যে ছুটি চাই। ক্যাম্পের বাইরে ঘুরতে যাব।
পরের রোববারে ক্যাম্পের বাইরে যাওয়ার পেলাম! তবে একাই যেতে হবে আমাকে। আর ফিরে আসতে হবে সাঁঝ ঘনাবার আগেই।
.
রোববার দিন সকালে ডাক পড়ল কোয়ার্টার মাস্টারের কামরায়। একজোড়া পুরনো বুট, চটের মোজা আর ঢোলা হাফপ্যান্ট পেলাম। এরপর কোয়ার্টার মাস্টার জানাল, বাইরে
ঘুরতে যেতে পারি আমি। তবে বেশি দূর যেন না যাই। রাস্তা হারিয়ে ফেললে ফিরতে পারব না সময়মত। রুমে ফিরে পোশাক-আশাক পরার পর দেখাতে লাগল গ্রাম্য দফাদারের মত! যা হোক, সামরিক পোশাক পরেই ক্যাম্প ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম আমি। লুঙ্গি পরে স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল পায়ে যে বেরুতে হয়নি, তাতেই যথেষ্ট খুশি। প্যান্টের পকেটে দুটো শুকনো রুটি আর জলের বোতলও নিলাম!
আগেই ভেবে রেখেছিলাম, যে রাস্তা ধরে আমরা প্রথম দিন ক্যাম্পে এসেছিলাম, যাব তার উল্টো দিকে। র্যাম্পের ওপর দিয়ে হেঁটে বাইরে বেরিয়ে আসার পর মোড় নিলাম ডানে। ধূ-ধূ করছে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। এখানে-ওখানে মাটির ওপর তৈরি হচ্ছে ধুলোর ঘূর্ণি। যতদূর চোখ যায় জনমানুষের চিহ্নও নেই কোথাও। ট্রেইল ধরে হাঁটতে লাগলাম। হাঁটছি তো হাঁটছিই। তীব্র গরমে ফেটে যেতে চাইছে তালু। একটা গাছও নেই যে তার নিচে দাঁড়িয়ে জিরিয়ে নেব কিছুক্ষণ। অবশেষে কিছুটা সরু হয়ে এল তেপান্তরের মাঠ। ডানে-বাঁয়ে পাহাড়, মাঝে চওড়া ফালি জমি। ধীরে-ধীরে আবারও দূরে সরে যেতে লাগল পাহাড়ের সারি। হাঁটতে-হাঁটতে এসে হাজির হলাম প্রায় তিন কিলো ব্যাসার্ধের অতিকায় এক গোল চত্বরের মতন জায়গায়। বিশাল চত্বরটা জুড়ে অসংখ্য পাথরের টুকরো, ঝোঁপ-ঝাড়, আর ধুলোবালি। সামনে তাকিয়ে দেখলাম গোল চত্বর ছাড়িয়ে আবারও চেপে এসেছে পাহাড়সারি। আকাশে হেলে পড়ছে সূর্য। আরও সামনে বাড়লে সন্ধের আগে আর ফিরতে পারব না। আমার বেড়ানো এখানেই শেষ। তবে ফেরা যাবে না এখনই। রুটি-জল খেয়ে তারপর ধরব ফিরতি পথ। কোনও এক জায়গায় বসা দরকার এখন। ডানে তাকিয়ে দেখলাম বেশ কিছুটা দূরে পাহাড়ের গোড়ায় শিরীষ গাছের মাথা দেখা যাচ্ছে। বিরাট লম্বা কাণ্ডের আগায় অল্প কিছু ডাল-পাতা। এগুতে লাগলাম ওদিকেই। কাছে গিয়ে দেখি অনেক পুরনো একটা ট্রেইল পাহাড়ের ঢাল বেয়ে এঁকেবেঁকে উঠে গেছে ওপর দিকে। ট্রেইলের দুদিকে ফণিমনসার গাছ, আধা শুকনো কাটা ঝোঁপ, উলুখাগড়ার মত ঘাসের গোছা, তবে লম্বায় অনেক খাট। খুব কাছ থেকে ভাল করে লক্ষ না করলে বোঝা যায় না ট্রেইল আছে ওখানে। উঠতে লাগলাম ট্রেইল বেয়ে। এত দূর যখন এলাম, দেখিই না ওপরে কী আছে?
ঘণ্টাখানেক হেঁটে উঠে এলাম পাহাড়ের মাথায়। পাহাড়চুড়ো একরকম চ্যাপ্টাই বলা চলে। সামনে কতদূর যে গেছে, তার ঠিক নেই। ফুট পঞ্চাশেক দূরে অতএব চিহ্নের মত তিনটে. আকাশ ছোঁয়া মহুয়া গাছ। পাহাড়ের এপাশের ঢালের গোড়া থেকে ত্রিশূলের মত নিরেট কালো পাথরের তিনটে শৈলশিরা বেরিয়ে ধীরে-ধীরে মিশে গেছে বিরাট চওড়া সমভূমিতে, তারপর আবারও পাহাড়। ভীষণ অবাক হয়ে দেখলাম, এই উপত্যকা ছাড়িয়ে ওদিকের পাহাড়সারির কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড এক তোরণ। দরজা-টরজা খুলে পড়ে গেছে কবেই! এখন হাঁ করে আছে এত্তবড় চৌকোনা ঘন অন্ধকার খোপ। দুপাশে উঁচু পাথরের বেদীর ওপর স্ফিংসের মত পশুর মাথাভাঙা মূর্তি। তোরণের দুদিক থেকে শুরু হয়েছে আদ্যিকালের ভীম মোটা ভাঙা-চোরা পঁচিল। পাচিলের ওপাশে অসংখ্য দালানের ধ্বংসাবশেষ। একসময় দোতলা-তিনতলা উঁচু ছিল দালানগুলো। কোনও কোনও দোতলা আধভাঙা হয়ে টিকে আছে এখনও। হা-হা করছে ওগুলোর জানালা-দরজার খোদল, রেলিং-ভাঙা বারান্দা।
দাঁড়িয়ে তন্ময় হয়ে আদ্যিকালের পোড়ো দুর্গ নগরী দেখছি, ঠিক সেই সময় বাঙ্ময় হয়ে উঠল পরিবেশ। ফিরে তাকালাম মহুয়া গাছগুলোর দিকে। ঝোঁপঝাড়ে ঢাকা গাছগুলোর গোড়া। শব্দটা আসছে ওদিক থেকেই। পায়ে পায়ে গেলাম গাছগুলোর দিকে। ঝোঁপের কাছাকাছি আসতেই চোখে পড়ল তিন গাছের মাঝখানে ফাঁকা জায়গায় শুকনো ডাল ভেঙে খড়ির টুকরো বানাচ্ছে চটের লেঙটি পরা বুড়ো মতন এক লোক। পায়ের নিচে ফেলে ডান হাত দিয়ে ভাঙছে ডালপালা। কনুই থেকে বাঁ হাতটা কাটা! বাঁ কানের লতিতে ঝুলছে ছোট্ট লোহার রিং। ইয়া লম্বা দাড়িতে জট পাকিয়ে গেছে, মাথা গড়ের মাঠ। একটাও চুল নেই ওখানে। পুরো কপাল জুড়ে সিঁদুর-চন্দন লেপা, গলায় ঝুলছে তিনপল্ল বরুই সাইজের কুঁচফুলের মালা। কুঁচফল যে এত বড় হতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস হত না। অস্বাভাবিক শীর্ণ শরীর লোকটার। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে বুকের খাবাচি, কনুই, হাঁটু, গোড়ালির জয়েন্ট আর আঙুলের গাঁট! কোটরের ভেতর ঘোলাঘোলা লালচে ছানিপড়া চোখ।
এ কাপালিক সন্ন্যাসী। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা বইয়ে পড়েছি এদের কথা, চোখে দেখিনি কখনও। ভয়ঙ্কর নরপিশাচ এরা, সাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্যে পারে না এমন কিছু নেই!
মনে-মনে ভীষণ ঘাবড়ে গেলেও বাইরে প্রকাশ করলাম না সেটা। ভাবলাম, আমার গায়ের সামরিক পোশাক দেখে সমীহ করতে পারে কাপালিকটা। ভাবতে পারে আমার পেছনে আরও নোক আসছে। কাছে এগিয়ে গিয়ে হাত-জোড় করে নমস্কার করে লোকটার কাছ থেকে শুকনো ডালটা নিয়ে ভাঙতে লাগলাম। একটার পর একটা ডাল ভেঙেই যাচ্ছি। কিছুটা দূরে পাথরের ওপর বসে একদৃষ্টিতে আমার কাজ দেখছে লোকটা। এখন পর্যন্ত একটা শব্দও উচ্চারণ করেনি।
কয়েকটা মাত্র শুকনো ডাল। ভেঙে টুকরো করতে আর কতক্ষণ লাগবে! কাজ শেষ হলে টুকরোগুলো জড় করে চোখ তুলে তাকালাম সন্ন্যাসীর দিকে। ইশারা পেয়ে সন্ন্যাসীর পাশে পাথরটার ওপর বসলাম। নাকে এল শ্যাওলার গন্ধ। সারাদিন জল-কাদায় ডুবে থাকা মোষের গায়েই শুধু এমন বিদঘুঁটে গন্ধ হয়। তবে সোঁদা গন্ধের মত এই গন্ধের ভেতরও এক ধরনের মাদকতা আছে। সন্ন্যাসী জিজ্ঞেস করল, আপ কাঁহা কা রেহনেঅলা হ্যায়?
হিন্দি ভাষা মোটামুটি বুঝলেও ঠিকমত বলতে পারি না আমি। জবাব দিলাম, বাঙ্গাল মুলুক।
এরপর সন্ন্যাসী পরিষ্কার বাংলায় বললেন, এখানে এলেন কীভাবে? স্থানীয় লোকেরাই তো আসে না এ জায়গায়!
এখানে আসার পেছনের ইতিহাস ভেঙেচুরে বললাম আমি। সব শুনে উনি শুধু বললেন, এই কালান্তক যুদ্ধই শেষ করবে মানবজাতিকে। সেই যে শুরু হয়েছে আদ্যিকালে, এখনও চলছেই। সব মানুষ মেরে তারপর থামবে ওটা! ওই যে সামনে বিরাট নগরীর ধ্বংসাবশেষ দেখছেন? ওটার কারণও এই যুদ্ধ। লড়তে-লড়তেই শেষ হয়ে গেছে। ওখানকার সব লোক। সর্বশেষ যারা বেঁচে ছিল, দাস হিসেবে বিক্রি হয়েছে তারা। ওটা এখন হানাবাড়ি বা হানাশহর, শত শত বছর ধরে পড়ে আছে ওভাবেই!
বললাম, কেউ নেই তাই বা বলি কী করে? আপনি তো আছেন? তা ছাড়া, কোনও বাঙালি যে কাপালিক সাধু হয়, তাই তো কোনওদিন শুনিনি। আপনার দেশের বাড়ি কি ওপারে কোথাও?
আমার কথা শুনে মৃদু হাসলেন কাপালিক। বললেন, সব প্রশ্নের উত্তর তো দেয়া যাবে না, বাবা। বরং সামনের ওই খাণ্ডালার ব্যাপারে বলি। এখনকার যে ভাঙা দালান দেখছ, ওগুলোর কিছু-কিছু নবাব শাহ ইউসুফ জাইয়ের আমলের। বিরাট এক নগরী ছিল তখন ওটা। সে-ও তিন শ বছর আগের কথা। এই নগরী আসলে আগে থেকেই ছিল। তৈরি হয়েছিল প্রায় তিন হাজার বছর আগে। দণ্ডকের ছেলে অযোধ্যার রাজা হরীত প্রথম তৈরি করে এটা। বিখ্যাত রাজা হরিশ্চন্দ্রের পূর্বপুরুষ সে। হারীতের বাবা দণ্ড হলো রাজা খাণ্ডের ছেলে। তো এই দণ্ডের ছিল চরিত্র দোষ। সুন্দরী মেয়ে চোখে পড়লেই হলো। তাকে ধরে ধর্ষণ করবেই। সে কুমারী হোক কিম্বা বিধবা অথবা কুলবধু! দণ্ডের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে খাণ্ডের কাছে বিচার চাইল প্রজারা। রাজা দণ্ডকে বিয়ে দিয়ে শুক্র মুনির কাছে পাঠাল বিদ্যা শিক্ষা করে মন আলোকিত করার জন্যে। এই মুনি থাকত অরণ্যে। রাজকুমার দণ্ড ওই বনে যাওয়ার পর বনের নাম হলো দণ্ডকারণ্য। ওখানে একটা শহর বানাল দণ্ড, তারপর শুরু হলো তার বিদ্যা শিক্ষা। সারাদিন গুরুর ঘরে বসে লেখাপড়া করে, সন্ধের সময় কোনার ঘরে, অর্থাৎ নিজের কামরায়। জপতপ। এই শুক্র মুনির অব্জা নামে এক যুবতী মেয়ে ছিল। দেখতে শুনতে খুবই ভাল, অদ্ভুত সুন্দর তার দেহ-বল্লরী! একদিন মুনি গেল গহীন বনে সারাদিনের জন্যে তপস্যা করতে। দণ্ড বইখাতা বগলে নিয়ে উঠোন পেরিয়ে এসে দেখে গুরু নেই ঘরে। ওদিকে অব্জাকেও দেখা যাচ্ছে না কোথাও। অব্জাকে খুঁজতে-খুঁজতে তাকে পেল নীলাজ সরোবরের পাড়ে। স্নান সেরে কাঁখে জলের কলসি নিয়ে বাড়ি ফিরছিল অব্জা। ভেজা কাপড়ে বাঙময় হয়ে উঠেছে অব্জার শরীরের প্রত্যেকটি বাঁক। সূর্যের কিরণ পড়ে চকচক করছে সুন্দর গোলগোল হাত-পা। পড়ালেখা মাথায় উঠল দণ্ডের, ভুলে গেল জপতপের কথা। এই রমণীকে তার এখনই চাই! অব্জাকে দেহ-মিলনের প্রস্তাব দিল সে। অব্জা হলো শুক্র মুনির মেয়ে, কাণ্ডজ্ঞানের অভাব নেই তার। দণ্ডকে বলল, সম্পর্কে আমি আপনার গুরু বোন। এই দুর্মতি থেকে নিস্তার লাভ করুন, রাজন।
অব্জার কথা কানেও তুলল না দণ্ড। পথ আটকে পীড়াপীড়ি করতেই থাকল। শেষে অব্জা বলল, বেশ। আমাকে ছাড়া আপনার যখন চলছেই না, এক কাজ করুন তা হলে। বাবাকে বলুন আপনার সাথে আমার বিয়ে দিতে। তারপর করুন, যা করতে চান।
চোরা না, শোনে ধর্মের কাহিনী। দণ্ড হলো ধর্ষকামী পাষণ্ড, জোর করে রমণী সম্ভোগ করাতেই তার যত আনন্দ! অব্জাকে টেনেহিঁচড়ে ঝোঁপের আড়ালে নিয়ে ধর্ষণ করল দণ্ড। আঁচড়ে-কামড়ে বিনাশ সাধন করল তার ননীর মত শুভ্র তুকের। তারপর নিজ কামরায় ফিরে ফলমূল আর সোমরস খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ক্লান্তিতে।
ওদিকে সারাদিন তপস্যা করে বিকেলে ঘরে ফিরল মুনি। অব্জাকে হেঁড়ে গলায় ডেকে বলল খাবার দিতে। মুনি দেখল খাবার দেয়া দূরের কথা, অব্জা তার ঘর থেকে বেরই হচ্ছে না। মেয়ের কামরার দিকে এগিয়ে গেল মুনি। দরজার গোবরাটে দাঁড়িয়ে বাজখাই গলায় বলল, কন্যা, পিতৃ আজ্ঞা শিরোধার্য, ভুলে গেছ সেকথা!
কী আর করা? আলুথালু অবস্থায় অব্জা এসে দাঁড়াল বাবার সামনে। শুক্র মুনি দেখল অব্জার চোখ ফোলা, সারাগায়ে খামচি আর কামড়ের দাগ। রাগে ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল মুনির। বলল, আমি ওদিকে তপস্যায় প্রাণপাত করছি, আর এখানে রঙ্গলীলা করছ তুমি! পিতার অবর্তমানে অবৈধভাবে কামনা-বাসনা চরিতার্থ করা! আমি শুক্র মুনি! এত বড় কুলাঙ্গার, আমার কন্যা!
বাবার রাগ খুব ভাল করে চেনা আছে অব্জার। মরার আগে মা বলে গেছে, আর যাই করিস, কখনও বাবাকে রাগাসনি, বাছা। তা হলে কিন্তু মহা সর্বনাশ হবে!
পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যা ঘটেছে, সব খুলে বলল অব্জা।
এইবার দণ্ডকে ডাকল মুনি।
গুরুদেবের হাঁকডাক শুনে বইখাতা বগলে করে সামনে হাজির হলো দণ্ড। যেন কিছুই হয়নি! আগের মতই ঠিকঠাক আছে সবকিছু।
দণ্ডকে মুনি বলল, শোন, দণ্ড, এতদিন এখানে থেকে এই শিক্ষা লাভ করেছ তুমি! এই তোমার চেতনা! দূর হও আমার সামনে থেকে। আমি যদি সত্যিই শুক্র মুনি হয়ে থাকি, তা হলে ভগবান যেন ভস্ম করে দেন তোমাকে, যাতে আর কোনওদিন কোনও অসহায় মেয়ের ক্ষতি করতে না পার।
শুক্র মুনি স্বয়ং অবতার। তার কথা শেষ হতে না হতেই আকাশ ফুড়ে ছুটে এল বজ্র। মুহূর্তের ভেতর পুড়ে ঝামা হয়ে উঠোনে পড়ে থাকল দণ্ড!
গর্ভধারণ করল অব্জা, জন্ম হলো হারীতের। প্রচুর ধন সম্পদের মালিক হয়েছিল এই হারীত। এক রাতে সে স্বপ্নে দেখল, মাঠের পর মাঠ সোনালি ধানের খেত। শীষে এত বেশি ধানের ছড়া যে নুয়ে পড়ছে গাছগুলো। কিন্তু ফসল তোলার আগেই হাড় জিরজিরে দুটো গরু খেয়ে সাফ করে দিচ্ছে একটার পর একটা ফসলের খেত। পর-পর তিন রাত একই স্বপ্ন! গণকদের ডেকে স্বপ্নের অর্থ জানতে চাইল হারীত। গণকেরা বলল, মহারাজ, ধন-রত্নে আপনি কুবেরকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছেন। ভয়ানক ঈর্ষাকাতর এই যক্ষ দেবতা কুবের। সম্পদ বাঁচাতে চাইলে একটা মন্দির তৈরি করে গোমুখী যক্ষকে উৎসর্গ করুন। গোমুখীই তখন আগলে রাখবে আপনার যত ধন-সম্পদ। গোমুখী যেখানে থাকে, সেখানে কখনও যায় না কুবের। তবে জায়গা নির্বাচনের বিষয় আছে। চারদিকে পাহাড় ঘেরা উপত্যকার এক অংশে, যেখানে পাহাড়ের প্রান্ত থেকে ত্রিশূলের মত তিনটে শৈলশিরা বেরিয়েছে, তার ঠিক উল্টোদিকে বানাতে হবে গোমুখী যক্ষের মন্দির।
এর কারণ, পৃথিবীতে নেমে আসার সময় ওখানেই প্রথম পা রেখেছিল গোমুখী। মন্দির তৈরি হলে পর এক শ মাদী মোষ বলি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করা হলো গোমুখীর মূর্তি। ভেট হিসেবে দেয়া হলো এন্তার সোনা-রুপো, দামি-দামি রত্ন। তারও, অনেক পরে শিশুনাগ বংশের রাজা মহাপদ্ম নন্দ এখানে করেছিল শহরের পত্তন। ঘোষণা করেছিল, এই নগরীতে রক্তপাত নিষিদ্ধ। কোনও সেনাবাহিনী আনা যাবে না এখানে। হাত দেয়া যাবে না মন্দিরের ধন-রত্নে। এরপর মৌর্য সম্রাট বিন্দুসার এখানে গড়ে তোলে বিরাট এক দুর্গ নগরী। ততদিনে ফুলে ফেঁপে উঠেছে মন্দিরের রত্ন ভাণ্ডার।
ভালই চলছিল সবকিছু, তবে গোল বাধল মৌর্য সম্রাট বৃহদ্রথের সময়ে। বিন্দুসারের অধস্তন সপ্তম পুরুষ এই বৃহদ্রথ। ঠিক সেসময় ব্যাকট্রিয়ার রাজা গ্রিক বীর ডেমিট্রিয়াস আফগানিস্তান আক্রমণ করে কাবুল থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত দখল করে বসল। তার মূল লক্ষ্য এখন পাটলিপুত্র বা বিহারের সম্রাট বৃহদ্রথ! চারদিকে সাজ-সাজ রব, বাজছে যুদ্ধের দামামা। মৌর্য বংশ তখন পড়তির দিকে। টাকা নেই রাজকোষে। ওদিকে যুদ্ধের জন্য চাই কোটি-কোটি টাকা। বৃহদ্রথ পাটলিপুত্র থেকে চলে এল এই নগরীতে। উদ্দেশ্য মন্দিরের গর্ভগৃহ ভেঙে অন্তত অর্ধেক ধন-রত্ন হাতিয়ে নেয়া। মন্দিরের পুরোহিতরা পইপই করে নিষেধ করল সম্রাট যেন এই কাজটি না করেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা! বৃদ্ৰথকে তখন যমে ধরেছে!
সেই ক্রান্তিলগ্নে বিশাল এক কুচকাওয়াজের আয়োজন করল বৃহদ্রথের সেনাপতি পুশ্যমিত্র শুঙ্গ। হাজার বছরের নিয়ম ভেঙে এখানেই জড় করল মৌর্য সেনাবাহিনীর সব সদস্য। নগরীর তোরণের সামনে উঁচু ম্যারাপের ওপর বসল বৃহদ্রথ। উদ্দেশ্য, গ্রহণ করবে সেনাবাহিনীর অভিবাদন। কুচকাওয়াজ চলাকালেই পুশ্যমিত্র আর তার অনুসারীরা ম্যারাপের ওপর খুন করে ফেলল সম্রাট বৃহদ্রথকে। নিজেকে মগধের সম্রাট ঘোষণা করল শুঙ্গ বংশের পুশ্যমিত্র। ভয়ানক পরধর্ম বিদ্বেষী ছিল এই শুঙ্গ ব্রাহ্মণেরা। মৌর্যরা ছিল বৌদ্ধ। সূচনা হলো বৌদ্ধদের ওপর সীমাহীন নিপীড়নের প্রথম কাহিনীর। মন্দির গর্ভে গোমুখীর মূর্তি সরিয়ে বসানো হলো কুম্ভন যক্ষের মূর্তি। যক্ষরা ভাল-মন্দ দুধরনেরই হয়। কুম্ভন। হলো রক্তপিপাসু এক ভয়ঙ্কর অপদেবতা! কুঞ্জন দেবতার পায়ের নিচে থাকে লোহার দরজা আঁটা কষ্টিপাথরের তৈরি কাল-কুঠুরি। আট-দশ বছরের ছেলেদের স্নান করিয়ে, ভাল মন্দ খাইয়ে, দামি পোশাক পরিয়ে সিঁদুর-চন্দন লেপে এই কাল-কুঠুরিতে ঢুকিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয় দরজা। খেতে না পেয়ে ধীরে-ধীরে শুকিয়ে মরে তারা। ক্রমাগত সাত দিন ধরে শোনা যায় তাদের কান্নার আওয়াজ। বাইরে বেরোবার জন্যে মাথা কুটে মরছে লৌহ-কপাটে! এখানেই শেষ নয়। পুশ্যমিত্র তেঁড়া পেটাল, প্রতিটি বৌদ্ধ পুরোহিতের কাটা মাথা এনে। দিলে দেয়া হবে এক শ স্বর্ণমুদ্রা। রাতারাতি উজাড় হয়ে গেল পাঁচ শ বৌদ্ধাশ্রমের হাজার-হাজার ভিক্ষু! শত-শত। বৌদ্ধ শিশু এনে ভরে দেয়া হলো কাল-কুঠুরিত্নে।
বাবারও বাবা থাকে। ডেমিট্রিয়াস, যাকে পুরাণে বলা হয়েছে ধর্মমিতা, সে এগিয়ে এল এই ক্রান্তিলগ্নে। গ্রিক দেবী অ্যাথিনার পূজারী ডেমিট্রিয়াস। অতি সূক্ষ্ম এর রুচিবোধ। এন্তার সুশৃঙ্খল গ্রিক পদাতিক আর দুর্ধর্ষ মোঙ্গলীয় ঘোড়সওয়ারে বোঝাই তার সেনাবাহিনী। ডেমিট্রিয়াসের বাহিনীর সামনে খড়কুটোর মত উড়ে গেল পুশ্যমিত্রের ধুতি পরা, অর্ধ-উলঙ্গ, খালি পায়ের বিহারী সৈন্যের দল। অবস্থা বেগতিক দেখে পাটলিপুত্র ছেড়ে পালাল পুশ্যমিত্র। পথে পড়ল বুদ্ধগয়া। এখানেই বিশাল এক ডুমুর গাছের নিচে বসে দশ বছর ধ্যান করে বোধি বা জ্ঞান লাভ করেন গৌতম বুদ্ধ। প্রচার শুরু করেছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের। পুশ্যমিত্রের জন্মের চার শ বছর আগের ঘটনা সেটা। পুশ্যমিত্রের সাথে তখনও জনাবিশেক দেহরক্ষী ছিল। ঘোড়ার পিঠে বয়ে নিয়ে যাচ্ছিল অজস্র ধন-রত্ন। সে ভাবল, নেড়েদের বিনাশ পুরোটা হয়নি। এখনও। শেষ বেলায় মহা-পবিত্র এই বুদ্ধগয়া ধ্বংস করে তারপর উত্তরে কোথাও গিয়ে আশ্রয় নেব। সঙ্গে যা টাকা পয়সা আছে, সেগুলো খরচ করে গড়ে তুলব অজেয় সেনাবাহিনী! তবে তার আগে চরম শিক্ষা দিতে চাই বৌদ্ধদের। মৌর্য সম্রাট ছাড়া অন্য কাউকে মানতেই চায় না এরা। এইবার বুঝবে পুশ্যমিত্রের ব্রাহ্মণ্যবাদ কী জিনিস! জয়, বাবা কুম্ভন যক্ষ, বলে বোধিবৃক্ষের দিকে লোকজন নিয়ে রৈ রৈ করে তেড়ে গেল সে। তবে গাছের গোড়ায় ছোট্ট মন্দিরটার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। এ কী! মন্দিরের ভেতর বুদ্ধের মূর্তির সামনে মেঝের ওপর হাঁটু মুড়ে বসে থাকা এই অপূর্ব রূপসী যুবতীটি কে? এত সুন্দর মানবীও আবার জন্মায় নাকি! এর ওপর থেকে তো চোখই সরানো যাচ্ছে না! দণ্ডের মত পুশ্যমিত্রেরও কাণ্ডজ্ঞান লোপ পেল। সব ভুলে লুটিয়ে পড়ল যুবতীর পায়ে। নিজেকে সমর্পণ করে বলল, প্রেম দাও, প্রিয়ে। তার বিনিময়ে নিয়ে নাও আমার যত ধন-রত্ন।
মৃদু হেসে যুবতী বলল, শুধুই ধন-রত্ন! তোমার হৃদয় দেবে না আমাকে?
খালি হৃদয় কেন? আমার প্রাণটাই তো তোমার, প্রিয়ে।
সত্যিই প্রাণ দিতে চাও? ঠিক বলছ তো?
অবশ্যই সত্যি বলছি, স্বর্গের দেবী। আমার হৃদয়,
আমার প্রাণ-এসবই এখন তোমার। তোমার প্রেমে আত্মাহুতি দিয়েছি আমি!
এই যুবতী আসলে ছিল ক্রিমিশা যক্ষ স্বয়ং। ক্রিমিশা চাচ্ছিল নিজের মৃত্যু নিজেই ডেকে আনুক পাষণ্ড পুশ্যমিত্র, যাতে আত্মহননের দায়ে অনন্তকাল নরকবাস হয় তার। তৎক্ষণাৎ ভয়ঙ্কর পিশাচের রূপ ধরল ক্রিমিশা, চড়চড় করে পুশ্যমিত্রের বুক চিরে একটানে বার করে আনল তার হৃৎপিণ্ড। কচকচ করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলল সেটা। এরপর ঘোড়ার পিঠে বসা বিশজন দেহরক্ষীর দিকে ছুঁড়ে মারল পুশ্যমিত্রের প্রাণহীন ছিন্নভিন্ন দেহ। হা-হা করে হেসে উঠল আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে। বাক্স-পেটরা ফেলে পড়িমরি করে ছুটল দেহরক্ষীর দল। কাকা, আপন প্রাণ বাঁচা! পিছু ধাওয়া করল পিশাচী। পেছন থেকে পিঠের ভেতর দিয়ে হাত ভরে টেনে বার করে আনল সব কটার কলজে। জড়সহ খেয়ে ফেলল সবগুলো হৃৎপিণ্ড!
এরপর ডেমিট্রিয়াস বা ধর্মমিতা পাটলিপুত্র ছেড়ে এল এখানে। ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল হাজার বছরের প্রাচীন নগরী। বিহারী সৈন্যদের মৃতদেহে গজাল মেরে ঝুলিয়ে রাখল পাঁচিলের গায়ে। শুরু হলো চিল-শকুনের মচ্ছব! তবে মন্দিরটা রেখে দিল। ঢকলই না ওখানে। দেব-দেবীর মন্দির ধ্বংস করা গ্রিক রণনীতি বিরোধী! সেই সাথে যক্ষ কুম্ভন আর শত-শত বলির-পাঁঠা হওয়া প্রেতাত্মার পাহারায়, মন্দিরের গোপন কুঠুরিতে রয়ে গেল অজস্র ধন-রত্ন!
এ পর্যন্ত বলে থামল কাপালিক।
কখন যে পাটে বসেছে সূর্য, খেয়ালই করিনি। তৎক্ষণাৎ রওনা হলেও ক্যাম্পে পৌঁছতে হয়ে যাবে মাঝরাত দেখলাম অস্তগামী সূর্যের দিকে তাকিয়ে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে কাপালিক। লক্ষ করলাম, সন্ন্যাসীর বাঁ কানের লতিতে তিরতির করে কাঁপছে লোহার ছোট্ট একটা রিং। মনে হলো হাজার প্রশ্ন করলেও এখন আর মুখ খুলবে না মানুষটা। রুটিদুটো আর জল খেয়ে ফিরতি পথ ধরলাম আমি।
চার
মাঝরাত হলো ক্যাম্পে ফিরতে-ফিরতে। ভাগ্য ভাল, আকাশে ছিল চাঁদ। ঊষর মরু এলাকায় চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যায় সবকিছু। না হলে, পথ চিনে ফিরতে পারতাম না ক্যাম্পে। চেক পোস্টে আটকাল আমাকে। সারারাত থাকতে হলো ওখানেই। পরদিন বেস কমাণ্ডারকে বললাম, নতুন জায়গা। রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম। হালকা শাস্তি দেয়া হলো আমাকে। পুরো ক্যাম্প ঘিরে দশ চক্কর মারতে হলো। তারপর আবার যে কে সেই। ট্রেনিং আর ঘরে বসে থাকা, ঘরে বসে থাকা আর ট্রেনিং। এভাবেই পেরিয়ে গেল আরও দুসপ্তাহ। এ সময়টায় মর্টার শেলিং আর মাটিতে মাইন পাতা শেখানো হলো আমাদেরকে। এরই ভেতর আরও দু শ নতুন রিক্রুট এসে হাজির। দলে-দলে মুক্তিযুদ্ধে নাম লেখাচ্ছে। বাঙালি ছেলেরা এখন। জায়গায় হয় না ব্যারাকে। সারি-সারি তাঁবু পড়ল পুরো উপত্যকা জুড়ে। কুচকাওয়াজের ভেতর দিয়ে শেষ হলো ট্রেনিং। আয়োজন করা হলো উন্নতমানের খাবারের। অর্থাৎ পোলাও, আলুর চপ, আর চর্বি দিয়ে ভোলার ডাল রান্না! মাঝে একদিন ছুটি, এরপর রণাঙ্গন!
কোয়ার্টার মাস্টারকে ধরে পড়লাম আমি। আবারও একদিনের ছুটি চাই। শেষবারের মত ঘুরে দেখতে চাই জায়গাটা। জীবনে কখনও তো আর আসা হবে না। রণাঙ্গনে কে মরে, কে বাঁচে, তার নেই ঠিক। বিষয়টা কোয়ার্টার মাস্টারও বুঝল। বলল, ঠিক আছে, যাও। তবে ভোরে ভোরে যাবে, ফিরে আসবে সন্ধের আগেই। সামাঝ গায়া না?
বললাম, জী, ওস্তাদজি। বিলকুল সামাঝ লিয়া।
.
পরদিন সকালে সূর্য যখন উঠি-উঠি করছে, রওনা হলাম তখনই। রাতের খাবার থেকে রুটি বাঁচিয়ে রেখেছি। জলের। বোতলসহ পকেটে ভরে নিলাম ওগুলো। এরপর হাঁটা ধরলাম। ত্রিশূল পাহাড়ের পথে। এক মাসেরও বেশি ধরে ট্রেনিং করেছি। দৌড়-ঝাঁপ-ক্রলিং, অবস্ট্যাকল পেরনো-বাদ যায়নি কিছুই। হনহন করে হাঁটতে লাগলাম। মাত্র আড়াই ঘণ্টার মাথায় পৌঁছে গেলাম পাহাড়ের ওপর অতএব মহুয়া গাছগুলোর কাছে। কিন্তু কোথাও কেউ নেই। গাছগুলোর মাঝখানে ঘেসো জমিনের ওপর কাঠের ছাই-কয়লা, মেটে আলুর খোসা। পাহাড়ের ঢালে এখানে-সেখানে ভুসভুসে মাটিতে হয় এই মেটে আলু। সন্ন্যাসীর জীবন তো দেখছি ভীষণ কৃচ্ছতার!
ওখানেই পাথরের চাঁইয়ের ওপর বসে খেলাম রুটি-জল। পরে খাব বলে বাঁচিয়ে রাখলাম কিছুটা। খাণ্ডালার দিকে হাঁ। করে চেয়ে থাকলাম অনেকক্ষণ। কিন্তু কোথায় সেই কাপালিক সাধুবাবা? এখনও অনেক জানার বাকি রয়ে গেছে তাঁর কাছ থেকে। মনে নানান চিন্তা। দেখব নাকি ওই হানাবাড়িতে গিয়ে কী আছে ভেতরে, নাকি ফিরে যাব। ক্যাম্পে? কী জানি অজানা কী বিভীষিকা ওঁৎ পেতে আছে। ওখানটায়! সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে উঠে দাঁড়ালাম। অদম্য কৌতূহল হচ্ছে খাণ্ডালার তোরণের কাছে গিয়ে উঁকি দিয়ে ভেতরটা দেখার। যে শৈলশিরাগুলো ত্রিশূলের মত ছড়িয়ে আছে, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নামতে যাব তার গোড়ায়, ঠিক সেই সময় খনখনে গলায় পেছন থেকে কে যেন বলল, ওদিকে কোথায় চললে, বাবা?
ঝট করে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। দেখতে পেলাম আগের সেই কাপালিককে। হালকা হাওয়ায় দোল খাচ্ছে কটা রঙের ইয়া লম্বা জটা দাড়ি। বললাম, আরে, সাধুবাবা, আপনি! আপনার খোঁজেই তো এখানে আসা!
তা-ই। ঠিক আছে, উঠে এসো এখন। বসা যাক গাছের নিচে ওই পাথরের চাঙড়টার ওপর, কেমন?
চাঙড়ের ওপর বসলাম দুজনে। কাপালিক বলল, আমার খোঁজে তো কেউ আসে না। তুমি এলে যে বড়?
কী আর বলব, সাধুবাবা? যে গল্প আপনি শোনালেন, তার শেষ না শুনে তো যেতে পারি না। আজকের দিনটাই শুধু আছি, এখানে। কালকেই চলে যাব যুদ্ধে। তারপর কী হবে, কে জানে!
বেশ, শোনো তা হলে। তবে একটা অনুরোধ রাখতে হবে।
কী অনুরোধ?
আমাকে কোনও ব্যক্তিগত প্রশ্ন করা যাবে না, ঠিক আছে?
আজ্ঞে, বুঝেছি। শুরু করুন এখন। আমাকে আবার সন্ধের আগেই ক্যাম্পে ফিরতে হবে। কড়া নির্দেশ আছে।
ডেমিট্রিয়াস বা ধর্মমিতা হয়তো আরও কিছুদিন থাকত এখানে। তবে সেটা আর সম্ভব হলো না। প্রথমে গুটিবসন্ত, তারপর ওলাওঠা। এই দুই মহামারীতেই উজাড় হয়ে গেল লাখ লাখ নারী-পুরুষ। সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেল ঝর্না, কুয়ো, আর পুকুরের জল। পূতিগন্ধময় হয়ে উঠল বিশাল এই ঐশ্বর্যশালী নগরী। ডেমিট্রিয়াস তো গেলই, সেই সাথে চলে গেল তখনও যারা বেঁচে ছিল। দুএকজন যারা থেকে গিয়েছিল, কী এক বিচিত্র কারণে এক রাতেই মারা পড়ল। চির অভিশপ্ত হয়ে গেল এ শহর। হয়ে উঠল লাখো প্রেতাত্মার এক জান্তব পিশাচ নগরী! রক্তপিপাসু হয়ে উঠল এর প্রতিটা সিঁড়ি, খাম্বা, বারান্দা আর দালান! রাজ্যপাট হারিয়ে অনেক রাজাই পরিবার-পারিষদ নিয়ে এখানে এসে থাকার চেষ্টা যে করেনি, তা না। তবে নগরীতে ঢুকে বাস করতে পারেনি কেউই। প্রথমে তোরণের বাইরেই তাঁবু খাটাত সবাই। ইচ্ছে, ভেতরটা পরিষ্কার করে বাসযোগ্য হলে, পরে ঢুকবে। তবে তারও আগে জল চাই তাদের। শহরের ভেতরের ইঁদারা কিম্বা ঝর্না থেকে স্বচ্ছ জল নিয়ে এসে খেলে পরদিন দেখা যাবে অর্ধেকের বেশি লোক বিছানা থেকে আর উঠতেই পারছে না! কী এক অজানা অসুখে ধরাশায়ী হয়ে গেছে তারা। এভাবেই পেরিয়ে গেল দেড় হাজার বছরেরও বেশি! কোনও-কোনও তান্ত্রিক ধন-রত্নের লোভে পড়ে কুম্ভন যক্ষের মন্দির পর্যন্ত গিয়েছিল। কিন্তু রত্নের চেহারাও কেউ দেখেনি। অপঘাতে মৃত্যু হয়েছে সব কটার।
শেষমেশ এখানে এসে হাজির হলো নবাব শাহ ইউসুফ জাই। এক লাখ লোক এনে তাঁবু ফেলল উপত্যকায়। শুরুতেই ইঁদারা খুঁড়িয়ে ব্যবস্থা করল পরিষ্কার জলের। এরপর দিনের আলোয় কারিগরদের পাঠাল নগর সাফ সুতরো করে, দালান-কোঠা ঠিক করার জন্যে। খাটতে লাগল হাজার-হাজার লোক। সে এক এলাহী কাণ্ড। কিন্তু যেভাবে ভাবা হয়েছিল, সেভাবে কাজ এগুল না। কিছুক্ষণ কাজ করার পরেই কাহিল হয়ে পড়ছে কারিগরেরা। ওদিকে সারাদিনে যেটুকু পরিষ্কার করা হয়, রাতের বেলা এলোমেলো হয়ে যায় সবকিছু। পরদিন সকালে আবার যে কে সেই! বিরাট ফাঁপরে পড়ল ইউসুফ জাই। পাটনায় ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। ওখানে সম্রাটের প্রিয় সুবাদার বসে আছে। দিল্লী থেকে ফরমান আনিয়ে ওই জায়গাটাকেই বেছে নিয়েছে সে। কাজেই তার নিজের থাকতে হবে এখানেই। কী করা যায় ভেবে অস্থির। হয়ে গেল সে। ওদিকে দিন-দিন কমে যাচ্ছে কাজের লোক। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, এ হলো জিনের শহর। হযরত সুলায়মানের সময় থেকেই এখানে নাকাবন্দি হয়ে আছে শয়তান জিনের দল! মাত্র পনেরো দিনে নেই হয়ে গেল অর্ধেক লোক। চিন্তায় কাহিল ইউসুফ জাই। ঠিক সেই সময় হাজির হলো এক চট পরা নাগা সন্ন্যাসী। অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ঘরের ছেলে। লেখাপড়াও শিখেছে। তবে ভবঘুরে ধরনের। বাউণ্ডলে হয়ে সাধু-সন্ন্যাসীর পিছে-পিছে ঘুরে বেড়ানোই এর কাজ। একবার এক বিহারী কাপালিকের সাথে দেখা হয় তার। বৎসরকাল তার পিছে লেগে ছিল ছেলেটা। তার কাছ থেকেই প্রথম জানতে পারে এই নগরী আর এন্তার ধন-রত্নের কথা। তাকে সাধু জানায়, একমাত্র মন্ত্র-সিদ্ধ কাপালিক ছাড়া ওই নগরীতে ঢোকার সাধ্য কারও নেই। ধন-রত্ন খুঁজে পাওয়া তো অনেক পরের কথা।
এরপর ছেলেটা দেখা পেল এক নাগা সন্ন্যাসীর। বহুকাল কাপালিক নাগাদের সাথে হিমালয়ে রয়ে গেল সে। এরপর নেমে এল নিচে, ইচ্ছে যক্ষের ধন-রত্ন বার করে নেয়া যায় কি না দেখা। এ কাজে প্রচুর ঝুঁকি আছে জেনেই এসেছে সে। কাপালিক গুরুর কাছ থেকে জেনেছে এখানকার সব। ঘটনা। এসব কথা অবশ্য ইউসুফ জাইয়ের জানা নেই। নাগা সন্ন্যাসীকে উপত্যকায় হাঁটতে দেখে তাকে ধরে নিয়ে এল। সিপাহীরা। এ রাস্তায় কখনও কাউকে যেতে দেখেনি তারা। এ লোক এখানে এল কী করে, এই তাদের জিজ্ঞাসা। এক কথা দুকথায় ইউসুফ জাইয়ের সাথে ভাব হয়ে গেল কাপালিকের। নবাব বাহাদুরকে সাহায্য করল সে। সাত দিন। উপোস দিয়ে গোমুখী যক্ষের উদ্দেশে বলি দিল জোড়া মাদী মোষ। তারপর কুম্ভন যক্ষকে সন্তুষ্ট করার জন্যে মন্দির চত্বরে লোহার খাঁচায় আটকে রাখল একজোড়া মাদী ঘোড়া। না খেতে পেয়ে ধীরে-ধীরে শুকিয়ে মারা গেল ওগুলো। এরপর ঘোড়ার দেহাবশেষ ঘুঁটের আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে ছড়িয়ে দিল শহরের কোণে-কোণে। মৃত মানুষের চর্বি দিয়ে হোমের আগুন জ্বেলে গোপন মন্ত্র পড়তে-পড়তে মহাযক্ষের পুজো করল পর-পর তিন রাত। দিনের প্রথম প্রহরে আগুনে জল ঢেলে ধোঁয়া ওঠা আধ-ভেজা ছাইয়ের ওপর রাখল তিনটে শ্বেত পদ্ম। তাকিয়ে থাকল এক দৃষ্টিতে ছাইচাপা আগুনের তাপে পদ্মফুলের পাপড়ি কুঁকড়ে যায় কি না দেখার জন্যে। টলটল করতে লাগল কমনীয় পাপড়ি। সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছে সে! এসব করতে-করতে পেরিয়ে গেছে এক মাস। ওদিকে মাঠের ভেতর তাঁবুতে থাকতে-থাকতে প্রায় শেষ হয়ে গেছে ইউসুফ জাইয়ের ধৈর্য। নগরী থেকে বেরিয়ে এসে কাপালিক তাকে বলল, মহারাজ, এইক্ষণে কাজ শুরু করতে বলেন আপনার কারিগরদের।
এইবার কাজ এগুতে লাগল চড়চড় করে। ধীরে-ধীরে বসবাসযোগ্য হয়ে উঠল ওই নগরী, সুপেয় হলো জলাশয়। ঠিক সেই সময় ঘটল অদ্ভুত এক ঘটনা। মন্দির চত্বরে সারাদিন হোমের আগুন জ্বেলে বসে থাকত কাপালিক। মাঝে-মাঝে শোনা যেত তার গম্ভীর কণ্ঠস্বর, ওম শিববাশদ্ভু…নমস্ততে…
মন্দিরে সারাদিন কাটালেও রাতে নগরীতে থাকত না কাপালিক। নিয়ম নেই। সে থাকত পাহাড়ের ওপর। গাছতলায়। কখন স্বপ্নের ভেতর নির্দেশ পাঠাবে যক্ষ, কাল কাটাতে লাগল সেই অপেক্ষায়।
ওদিকে কাপালিককে নবাব খুব পছন্দ করে দেখে হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরতে লাগল উজির সাহেব। ষড়যন্ত্রের জাল বুনল সে। নবাবের কসাইকে ধরে উপত্যকার গোরস্থান থেকে তুলে আনল সদ্যমৃত এক শিশুর লাশ। ছুরি দিয়ে এমনভাবে লাশটার গলা কাটল যে, দেখে যে কারও মনে হবে জবাই করে হত্যা করা হয়েছে বাচ্চা ছেলেটাকে। এরপর একটা শুয়োর মেরে পেট চিরে বার করে ফেলল ওটার সব নাড়িভুড়ি। শুয়োরের পেটের ভেতর ছেলেটার লাশটাকে রেখে আবারও পেট সেলাই করে কসাইকে দিয়ে পাঠিয়ে দিল মন্দির চত্বরে ফেলে রাখার জন্যে।
ভোর রাতে কসাই গিয়ে উজিরের নির্দেশ মত মন্দির চত্বরে ফেলে এল শুয়োরের দেহ। খুব ভোরে নামাজ পড়ে উজির-নাজিরসহ শহরের পথে হাঁটতে বেরুত নবাব। মন্দিরের কাছাকাছি এসে তার চোখে পড়ল মৃত শুয়োরের দেহ। ঘটনা কী জানতে কাছে এগিয়ে গেল নবাব। উজির তখন বলল, ধর্মাবতার, লক্ষ করেছেন, এই শুয়োরের পেট চিরে পরে আবার সেলাই করা হয়েছে ওটা! দেখে মনে হচ্ছে শুয়োর মেরে পুজোর ভেট চড়িয়েছে ওই কাপালিক। জঘন্য আর ভয়ানক নাপাক এদের কর্মকাণ্ড! পারলে এরা আস্ত মানুষকেও বলি দিয়ে ফেলে! শুয়োরটার পেট কেটে দেখা দরকার কী আছে ভেতরে, কী বলেন আপনারা? এই কথা বলে সাথের লোকদের দিকে তাকাল উজির।
সবাই বলল, খুবই ঠিক কথা। পেট চিরে দেখতে হবে কী আছে ওখানে।
মুচি ডেকে কাটা হলো শুয়োরের পেট। ভেতরে কাফনে জড়ানো ছোট্ট শিশু
দুফাঁক হয়ে আছে গলা!
বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগল উজির। বলল, ধর্মাবতার, দেখেন এই কাপালিকের অনাচার! মুসলমান শিশুর গলা কেটে শুয়োরের পেটের ভেতর ভরে দেবতার পায়ে অর্ঘ্য নিবেদন করেছে এই পাষণ্ড! এই অনাচার আল্লা সইবেন না! এর বিচার করেন আপনি! এক্ষুণি, এই মুহূর্তে!
দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল ইউসুফ জাই। কী করবে সেইটেই বুঝতে পারছে না। আর ঠিক তখনই ওখানে হাজির হলো কাপালিক। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উজির বলল, নগর কোটাল! গ্রেফতার কর এই বদমাশটাকে।
দুপুরে বিচার শুরু হলো কাপালিকের। সবার এক কথা: গর্দান নামিয়ে দাও ওর। আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে কাপালিক বলল, এ এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র। এসবের কিছুই জানি আমি।
অবশেষে রায় দিল নবাব। বলল, জঘন্য অপরাধ সঙ্ঘটিত যে হয়েছে এটা ঠিক। তবে একটা প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। সেইটে হলো, কাপালিক যদি নরহত্যা করে শুয়োরের : পেটের ভেতর সেই লাশ পুরে দেবতার উদ্দেশে ভেট চড়িয়েই থাকে, তা হলে শুয়োরের লাশ সবার সামনে ফেলে রাখবে কেন? এই কাজ তো করার কথা সঙ্গোপনে!
উজির তখন বলল, ধর্মাবতার, ওই শয়তান। সঙ্গোপনেই সবকিছু করতে চেয়েছিল। কিন্তু সময়ে কুলোয়নি। জানেন তো, এদের ভেতর লগ্ন-ফগ্ন বলে হাবিজাবি অনেক কিছু আছে।
ইউসুফ জাই বলল, ঠিক আছে, আপনার কথা অনুযায়ী ধরে নিলাম এই লোক দোষী। তবে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না তাকে। আসামী অতীতে আমাদের অনেক সাহায্য সহযোগিতা করেছে। তারপরেও প্রমাণে ফাঁক-ফোকর আছে। এর এক হাত কনুইয়ের নিচ থেকে কেটে ফেলা হবে। তারপর তাড়িয়ে দেয়া হবে এই নগরী থেকে। বিচার এখানেই শেষ আদালত মুলতবী ঘোষণা করা হলো।
উজিরকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই উঠে গেল নবাব। টেনে-হিঁচড়ে কাপালিককে মন্দির চত্বরে নিয়ে যাওয়া হলো। তলোয়ারের এক কোপে কনুই থেকে কাটা পড়ে গেল বাঁ হাত। এরপর অম্লজারকে ভিজিয়ে বন্ধ করা হলো রক্তঝরা। জখমের জায়গায় কাপড়ের টুকরো বেঁধে সৈন্যেরা নগর-তোরণের বাইরে বার করে দিল তাকে। বলল, আর কখনও এসো না এখানে। নির্বাসনে পাঠানো আসামীরা ফিরে এলে মৃত্যুদণ্ড অবধারিত নবাবও বাঁচাতে পারবে না তখন!
দূরের এক পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিল কাপালিক। সন্ধের দিকে বেহুশ হয়ে পড়ল প্রচণ্ড জ্বরে। ঠিক এই সময় দেখা দিল গরুমুখী যক্ষ। বলল, বাছা আমার, যে ধন-রত্বের জন্যে নিজের অঙ্গ পর্যন্ত খোয়ালে, তা তো কখনও পাবে না তুমি। চিরস্থায়ীভাবে অভিশপ্ত ওই ধন-রত্ন। তবে একটা বর তোমাকে দেব আমি। তুমি বেঁচে থাকবে শত-শত বছর। এই সময়ে যদি সম্পূর্ণ নির্লোভ এমন কাউকে পাও, আর সে স্বেচ্ছায় ধন-রত্ন তুলে আনতে রাজি হয়, তা হলে কিছুটা হলেও ওই ধন পাবে তুমি। তবে মনে রেখো, এমন লোক খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন। আর পেলেও সে এই কাজ করতে রাজি হবে কি না, সেটাও বড় একটা বিষয়!
স্বপ্নের ভেতরই কাপালিক বলল, দেবরাজ, আপনার বর শিরোধার্য! তবুও বলব, এত বড় অন্যায় হলো আমার ওপর! এর বিচার আপনি করেন।
যক্ষ তখন বলল, ওটা নিয়ে ভেবো না। শুধু তোমার তপস্যার কারণেই বাসযোগ্য হয়েছিল ওই নগরী। এইবার চিরদিনের মত ধ্বংস হবে। ওটা হবে প্রেত-যোনী আর নিষ্ঠুর যক্ষের শহর।
পরদিন রাতে প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পে থরথর করে কেঁপে উঠল পৃথিবী। ভেঙে খানখান হয়ে গেল নগরীর দোতলা তিনতলা দালান। এখানে-সেখানে ভেঙে পড়ল পাঁচিল, মাটির ভেতর পুরোপুরি সেঁধিয়ে গেল গোমুখী যক্ষের মন্দির! এর পরদিন ছড়িয়ে পড়ল মহামারী। মাত্র সাত দিনে উজাড় হয়ে গেল সব লোক। হা-হা করতে লাগল শূন্য শহর!
ব্যস, এতটুকু বলেই চুপ করে গেল কাপালিক। আবারও পশ্চিমাকাশে সূর্যের নিচে নগরীর দিকে তাকিয়ে ধ্যানমগ্ন হলো সে। তিরতির করে কাঁপতে লাগল বাঁ কানের ফুটোয় লোহার ছোট্ট রিং। বুঝলাম, প্রশ্ন করে কোনও লাভ হবে না। ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে এখন।
পাঁচ
ক্যাম্পে ফিরে এলাম সন্ধের আগেই। কাপড়-চোপড় গোছগাছ করে পরদিন সকালে আর্মি ট্রাকে চড়ে রওনা হলাম মুক্তিযুদ্ধ হেডকোয়ার্টারের উদ্দেশে। সেখান থেকে একটা দলের সাথে দিয়ে দেয়া হলো আমাকে। চলে গেলাম মেহেরপুর বর্ডারে। পর-পর দুটো অপারেশন করলাম আমরা। একবার স্যাবোটাজ করলাম মিলিটারি কনভয়। আরেকবার আক্রমণ করলাম এক শত্রু ছাউনিতে। এক প্লাটুন খান সেনা থাকার কথা ওখানে। তবে আমরা পেলাম মাত্র বারোজনকে। এরপর আমাদের দলকে পাঠানো হলো কাজীপুর বর্ডারে। দুটো দল একসাথে হয়ে ওপারের একটা ক্যাম্প আক্রমণের পরিকল্পনা করা হলো। সিদ্ধান্ত হলো মাঝরাতে হামলা করা হবে। ওপারে এক মহাজনের বাড়িতে গিয়ে জমায়েত হওয়ার কথা সবার। বিকেল থেকেই একজন, দুজন করে ফসলের মাঠের ভেতর দিয়ে ঘাস কিংবা বিচালির আঁটি মাথায় করে যেতে শুরু করল মুক্তিযোদ্ধারা। আঁটির ভেতর লুকানো হাতিয়ার, গন্তব্য মহাজনের বাড়ি।
আলের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছি আমি। মাথার ওপর খড়ের আঁটির ভেতর ত্রি-ইঞ্চ মর্টার গান। হঠাৎ বিকেলের পড়ন্ত আলোয় দূরে বাবলা গাছের নিচে দেখলাম অতি ক্ষীণ দেহের কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। আরে, এ তো সেই চট পরা কাপালিক! শরীরে কাঁপুনি উঠে গেল আমার। তাল সামলাতে না পেরে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। মচকে গেল পা। হাঁটতেই পারি না আর। দুজন ধরে নিয়ে এল এপারের ক্যাম্পে। আমাকে রেখে ফিরে গেল আবার। রাত নটার দিকে বিরাট কাঁচারি ঘরে গোস্ত-পরোটা খাওয়ার আয়োজন করল মহাজন। যুদ্ধে যাওয়ার আগে ভাল-মন্দ খাওয়াই নাকি রীতি! কে জানে, কে মরে কে বাঁচে? মুক্তিযোদ্ধাদের দুটো দলকে একসাথে বসিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে, ঠিক সেই সময় দরজা আটকে সরে পড়ল মহাজন। পুরো বাড়ি ঘিরে ফেলল খান সেনারা। ঘরে আগুন ধরিয়ে স্রেফ পুড়িয়ে মারল একত্রিশজন মুক্তিযোদ্ধাকে! শুধু বেঁচে থাকলাম আমি-বত্রিশ নম্বর!
ছয়
অন্য দলে যোগ দিলাম আমি। এখানে-সেখানে অপারেশন চালাতে-চালাতে একদিন গেলাম মালিথা গ্রামে। ভাবলাম, বড় মালিথার সাথে একবার দেখা করে আসি। মালিথাদের কাঁচারি ঘরে যখন পৌঁছলাম, তখন যোহর নামাজের সময়। কাঁচারি ঘরের দাওয়ায় জলচৌকির ওপর বসে ওজু করছে বড় মালিথা। মাথা-ঘাড় ঢাকা সেই চেকচেক উড়নি এখন আর নেই। দেখলাম চকচকে টাক মাথা বড় মালিথার, একটাও চুল নেই ওখানে। বাঁ কানের লতিতে ঝুলছে ছোট্ট লোহার রিং। তিরতির করে কাঁপছে ওটা!
পরিশিষ্ট
১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে আমার এক চাচা কমাণ্ডার ছিলেন। আমরা বলতাম সেকেন্দার চাচা। সেকেন্দার চাচার দলে সমীরণ সাহা নামে এক সহযোদ্ধা ছিল। এই সমীর ছিল সেকেন্দার চাচার ডান হাত। যেমন সাহসী তেমনি তার বুদ্ধি! রণাঙ্গনে বাঙ্কারের ভেতর বসেও ডায়েরি লিখত সমীর। ১৫ ডিসেম্বর বিকেলবেলা তাঁর দল নিয়ে কুষ্টিয়া শহরে ঢুকলেন চাচা। ক্যাম্প করলেন মীর মশাররফ হোসেন গার্লস হাইস্কুলে। সন্ধের সময় যখন রাতের রাধা-বাড়া চলছে, চুলোর পাশে বসে রেডিয়োতে আকাশবাণীর খবর শুনছেন চাচা, ঠিক সেই সময় পায়ে-পায়ে এগিয়ে এল সমীর। চাচাকে বলল, কমাণ্ডার, কলেজের ওদিকটা থেকে একটু ঘুরে আসতে চাই। যদি অনুমতি দেন, তো যাই এখন?
চাচা বললেন, আরেকটু বসো। খেয়ে-দেয়ে তারপর না হয় যেয়ো। আর এখন যাওয়াটাও ঠিক হবে না। কাল সকালের পর গেলেই ভাল করবে। আগে সারেণ্ডার করে নিক পাকিস্তান আর্মি, কী বল?
সমীর ওদিকে মাথা মুখ নিচু করে দাঁড়িয়েই আছে। চাচা দেখলেন, এই ছেলে যা চায়, তা করেই ছাড়বে। অনুমতি না দিলে পালিয়ে গিয়ে ঘুরে আসবে। অন্য সহযোদ্ধারা তখন বলবে, সমীর অনুমতি ছাড়াই বাইরে ঘোরা-ফেরা করে। হয়। তাকে শাস্তি দেন, না হয় আমাদেরকেও দেন সেই স্বাধীনতা! সমীরকে শাস্তি দেয়া সেকেন্দার চাচার পক্ষে সম্ভব নয়। চাচা বললেন, এখনই যেতে চাও? খেয়ে গেলে ভাল হত না?
জী, কমাণ্ডার, এখনই যেতে চাই। হাতিয়ার রেখে গেলাম। এই যাব আর আসব।
ঠিক আছে, বাবুর্চিকে বলব তোমার খাবার আলাদা করে যেন তুলে রাখে। এসে দেখা কোরো আমার সাথে, কেমন?
সেই যে গেল সমীর, ফিরল না আর! সারারাত প্রচুর। গোলাগুলি আর মর্টার শেলিং হলো।
পরদিন বারোটায় সারেণ্ডার করল খান সেনারা। প্রচুর খোঁজাখুঁজি করলেন সেকেন্দার চাচা। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না সমীরকে। তার হাতিয়ার মালখানায় জমা দেয়া হলো। কাপড়ের ব্যাগটা রয়ে গেল সেকেন্দার চাচার কাছে। ওটার ভেতর সমীরের ডায়েরি, দাঁতের মেসওয়াক, গায়ে মাখা সাবান, কাপড়-চোপড়, ধুন্দলের ছোবড়া আর কিছু টুকটাক হাবিজাবি।
তখন আমরা কুষ্টিয়া শহরেই থাকতাম। সবকিছু থেমে গেল, সহযোদ্ধারা ফিরে গেল নিজ-নিজ এলাকায়, আর সেকেন্দার চাচা এলেন আমাদের ওখানে বেড়াতে। সাথে করে নিয়ে এলেন সমীরের সবুজ রঙের ক্যানভাস কাপড়ের ব্যাগ। এরপর শুরু হলো নকশাল আন্দোলন, সর্বহারা, গণবাহিনী এইসব। এই ডামাডোলে হারিয়ে গেলেন সেকেন্দার চাচাও। ব্যাগটা রয়ে গেল রত্না আপার জিম্মায়। বেশ কয়েক বছর পর এক রাজাকার এমপির ছেলের সাথে বিয়ে হয়ে শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার আগে আলমারি সাফ করল আপা। সেই সময় আবারও আত্মপ্রকাশ করল সমীরের সবুজ ব্যাগ। এবার ওটাকে খুললাম আমি। পেলাম ওখানে যা ছিল, সবকিছু। দুপুরে খেয়ে-দেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তে লাগলাম সমীরের ডায়েরি। জানলাম, মুক্তিযুদ্ধের এক অজানা কাহিনী, যা কোনওদিন লেখা হবে না ইতিহাসে!
আছে ও নেই – অরণ্য সরওয়ার
সেদিন সকালে এক বৃদ্ধ এসে হাজির হলেন আমার কাছে। তিনি প্রায় কাতর স্বরে বললেন, চাচাজী, আমার একটা সাপের চাউট্টা (আঁচিলের আকৃতির এক ধরনের পরজীবী) দরকার। নাতিনডার খুব অসুখ, কবিরাজ কইছে, অসুধ বানাইতে সাপের চাউট্টা লাগব। লোকটার কথা শুনে বুঝলাম, তার ধারণা আমার বাড়িতে সাপের খামার জাতীয় একটা কিছু আছে। অনেকেই এমন ধারণা পোষণ করে থাকেন। কারণ সাপের সঙ্গে আমার সম্পর্ক সেই শৈশব কাল থেকে। এক অজানা আকর্ষণের ফলশ্রুতিতে বার বার আমি ওদের কাছে ছুটে যাই। কত কিছুই না করেছি ওদের নিয়ে। সাপ ধরা, সাপের ছবি তোলা, দিনের পর দিন এদের বিষয়ে বিভিন্ন বই পড়া। বিভিন্ন পত্রিকায় সাপের উপর আর্টিকেল আর গল্প লেখা-আমার এসব পাগলামির কথা তাই অনেকেরই জানা। সেই থেকে এই বৃদ্ধের মত অনেকের মনে। নানা ধরনের ধারণার জন্ম হয়েছে। কোথাও সাপ দেখা গেলে মানুষ আমার কাছে ছুটে আসে, একবার সাপে কাটা রোগী পর্যন্ত আমার বাড়িতে নিয়ে আসা হলো। এলাকার পল্লী চিকিৎসক আমজাত ডাক্তারের চেম্বারে সাপে কাটা রোগী আসার সাথে সাথে আমার কাছে খবর পাঠানো হয়। অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে আমাকে এসব বিষয় মোকাবেলা করতে হয়। কারণ আমি কোনও সর্প বিশারদ কিংবা পেশাদার ওঝা নই, সাপ আমার নেশা। সেদিন ওই বৃদ্ধ যা চেয়েছিল তা আমার কাছে না থাকলেও, যেখানে থাকতে পারে, আমি তাকে সেই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম।
সাপের পাশাপাশি আমার আর একটি ব্যক্তিগত আগ্রহের বিষয় হচ্ছে জিন। পৃথিবীর বুকে এদের অস্তিত্বের কথা মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ আল-কোরানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সেই ছোটবেলায় প্রথম জিনে ধরা মানুষ দেখেছিলাম নানা বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে। গ্রামের এক মহিলা দুপুর বেলা জঙ্গলে গিয়েছিল লাকড়ির সন্ধানে। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত বাড়ি ফিরে না আসায় লোকজন বনে ঢুকে তাকে প্রায় অচেতন অবস্থায় খুঁজে পায়। তখন তার শরীর জুড়ে প্রচণ্ড খিচুনি আর মুখ দিয়ে গেঁজলা ঝরছিল। নানা বাড়ির ঠিক পাশেই ছিল মহিলার বাড়ি। তাকে বাড়িতে নিয়ে আসার পর সবাই গেল দেখতে, সাথে আমিও। সেখানে যাওয়ার পর ওই মহিলার প্রচণ্ড খিচুনি আর ভয়ঙ্কর মুখচ্ছবি আমার ছোট্ট মনে দারুণ ভয় এনে দিল। এরপর প্রায়ই আমি নানা বাড়ির সামনের বিলের ধারে দাঁড়িয়ে ওপারের বনের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। ওই যে দূরে ঘন বন, ওখানে বাস করে ভয়ঙ্কর জিন, গেলেই ধরবে-কথাগুলো মনে আসতেই আমি এক দৌড়ে বাড়ির ভিতর চলে যেতাম। সেই আমার জিনের সঙ্গে প্রথম পরিচয়।
তারপর কৈশোরে একদিন হেঁটে যাচ্ছিলাম আমাদের গ্রামের কাদির মুন্সির বাড়ির পাশ দিয়ে। কাদির মুন্সি প্রয়াত পীর আলী নেওয়াজ মুন্সির ছেলে। জনশ্রুতি আছে আলী মুন্সির একাধিক অনুগত জিন ছিল। কাদির মুন্সিরও বাবার মত জিনের কারবার। প্রায়ই তার ওখানে জিনে ধরা রোগী নিয়ে আসা হয়। বাড়ির সামনে লোকজনের জটলা দেখে, সেদিকে এগিয়ে গেলাম। এগিয়ে গিয়ে উৎসুক জনতার কাঁধের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে যা দেখলাম তাতে অবাক না হয়ে পারলাম না। আট ন বছরের একটা মেয়েকে দুজন শক্ত সমর্থ লোক দুদিক থেকে ধরে রেখেছে। মেয়েটার চুল। এলোমেলো, চোখদুটি রক্তের মত লাল। সে ক্রমাগত চেঁচিয়ে চলেছে, যামু না, আমি যামু না, আমার লগে বাড়াবাড়ি করিস না, জানে মারা পড়বি। তখন কাদির মুন্সি এগিয়ে এসে নিজের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে মেয়েটার কড়ে আঙুল চেপে ধরল। সাথে সাথে সে কী গগন বিদারী চিত্তার-মুন্সি, তোর ক্ষতি হইব কইতাছি, আমারে ছাইড়া দে।
মুন্সির চেহারা ভাবলেশহীন। তিনি শীতল গলায় বললেন, মাইয়াডারে কোন জায়গা থাইক্যা ধরছছ আগে হেইডা ক।
মেয়েটি কিছু বলল না। মুন্সির নখ গম্ভীর হয়ে চেপে বসল মেয়েটির কড়ে আঙুলের পিঠে। সাথে সাথে চেঁচিয়ে উঠল, মাইয়াডা এমবি সাবের পুষ্কনির পার আইছিল দুপুর বেলা। হেইখান থাইক্যা ধরছি। ওটা আসলে আমাদেরই পুকুর। আমার বাবা ডা. ফজলুল করিম পাঠান এলাকার মানুষের কাছে এমবি (এম.বি.বি.এস-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ) সাহেব নামে পরিচিত। এখন দেখা যাচ্ছে মানুষের জগতের বাইরে জিনের দুনিয়ায়ও তার পরিচিতি রয়েছে! মেয়েটার অবস্থা দেখে আমি তখন হতবিহ্বল, ভেবেই পাচ্ছিলাম না। এই ছোট্ট বালিকা কীভাবে এসব কথা বলছে?
মেয়েটার (নাকি জিনের) সঙ্গে কথা বলার এক পর্যায়ে কাদির মুন্সি হুঙ্কার ছেড়ে বললেন, এই, মোস্তফা, বাঁশ ঝাড় থাইক্যা কয়টা কঞ্চি কাইট্যা লইয়া আয়। মোস্তফা দৌড়ে গিয়ে কয়েকটা কঞ্চি কেটে আনল। শুরু হলো কাদির মুন্সির দ্বিতীয় পর্যায়ের চিকিৎসা। সপাং-সপাং কঞ্চির আঘাত পড়তে লাগল মেয়েটির গায়ে, আমি আর ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না।
বাবা ছিলেন অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ। তার চিন্তা-চেতনার সমান বিচরণ ছিল বাস্তব আর পরাবাস্তবে। দেশের খ্যাতনামা চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁর যেমন নিয়মিত যোগাযোগ ছিল তেমনি সম্পর্ক ছিল বিখ্যাত আলেম-ওলামা, তান্ত্রিক ফকির আর পীর-এ-কামেলদের সাথে। মাঝে মধ্যে তিনি অদ্ভুত সব কাজ করতেন। একবার এক জিন সাধকের সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি গাজীপুরের এক প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে হাজির হলেন। বাড়ি খুঁজে বের করে নিজের পরিচয় দিতেই জিন সাধক যেন আকাশ থেকে পড়লেন, এই বিখ্যাত চিকিৎসককে গাজীপুরের কে-না চেনে? প্রত্যন্ত অঞ্চলের কত মানুষ জীবন বাঁচাতে ছুটে যায় ওঁর কাছে। এ মধ্যবয়সী-স্বাস্থ্যবান জিন সাধক তাঁকে সাধন কক্ষে বসিয়ে বললেন, স্যর, অজু ছাড়া ডাকলে জিনে আইৰ না, আপনে একটু বসেন আমি অজু কইরা আসি। সাধক অজু করতে চলে যাওয়ার পর বাবা ঘরটাকে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। জানালাগুলো ভোলা থাকায় তার কাজ সহজ হলো। (এ কাহিনি লিখছিলাম নদীর ধারে এক নির্জন ঘরের খোলা জানালার পাশে বসে। তখন রাত দশটা বিশ। মাত্র দুমিনিট আগে বিকট শব্দে জানালার পাশের একটি কলাগাছ পানিতে ভেঙে পড়ল, নিজের অজান্তে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল, চেয়ার ছেড়ে উঠে জানালা দিয়ে টর্চের আলো ফেলতেই দেখলাম, গাছটা পাতা ছড়িয়ে পড়ে আছে কচুরিপানার দামের উপর।) সাধকের সমস্ত ঘরের মধ্যে আসবাব বলতে একটা মাত্র কাঠের চৌকি।
কিছুক্ষণ পর জিন সাধক ঘরে ঢুকে সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে দিলেন। তারপর বিছানায় উঠে মোমবাতি জ্বালিয়ে সামনে রেখে পদ্মাসনে বসলেন। এই বিশেষ পরিবেশে যে কোনও মানুষের পক্ষে সামান্য হলেও ঘাবড়ে যাওয়ার কথা, কিন্তু বাবার নার্ভ ছিল ইস্পাতের মত কঠিন। তাই তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে গোটা বিষয়টা প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। চোখ বন্ধ করে অদৃশ্য জিনের উদ্দেশে সালাম দিলেন সাধক। সালামের প্রত্যুত্তরের সঙ্গে সঙ্গে গমগম করে উঠল সমস্ত ঘর। জিন আর সাধকের কথোপকথন চলল কিছুক্ষণ। তারপর বেশ কিছুটা সময় ধরে বাবার সঙ্গে জিনের প্রশ্নোত্তর পর্ব চলল। একসময় বাবাকে আশীর্বাদ করে বিদায় নিল জিন। আর তৎক্ষণাৎ তিনি ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন। বাইরে তখন জিনের সঙ্গে কথা বলার জন্য বেশ কয়েকজন মানুষ অপেক্ষমাণ। তাঁরা নানা সমস্যার সমাধান পেতে এখানে এসেছেন। তিনি তাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকে প্রথমে সমস্ত জানালা খুলে ফেললেন, এরপর চৌকিটাকে ধরে এক পাশে সরিয়ে রাখলেন। গোলাকার একটা গর্ত ভেসে উঠল সবার চোখের। সামনে। বাবা সেই গর্তের কাছে গিয়ে বললেন, বাইরে বেরিয়ে এসো, জিন বাবাজী, নইলে এখনই গরম পানি ঢেলে দেব। সাথে সাথে অতিকায় ইঁদুরের মত শীর্ণকায় এক যুবক বেরিয়ে এল গর্তের মুখ গলে। সাধক আর জিন দুটোই গিয়ে পড়ল বাবার পায়ে।
বিশ বছর পরের কথা। আমি তখন ইন্টারমিডিয়েট প্রথম বর্ষের ছাত্র, বাবা ষাট বছরের তরুণ! এই বয়সেও তিনি স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়ান বাইক নিয়ে, প্রায়ই রোগী দেখতে যান দূরবর্তী গ্রামে। এক সকালে তিনি আমাকে মোটরসাইকেলের পেছনে বসিয়ে রওনা দিলেন চরনগরদী গ্রামের দিকে। আমি ভেবে পেলাম না হঠাৎ তিনি আমায় নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন। চরনগরদী বাজারে পৌঁছে মসজিদের পাশে বাইক রেখে তিনি পার্শ্ববর্তী একটি চৌচালা টিনের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।
দরজার কড়া নাড়তেই পাকা আলেম টাইপের এক লোক বেরিয়ে এলেন। বাবাকে সালাম জানিয়ে তিনি আমাদের নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বাইরে যা দেখেছি ভিতরে সম্পূর্ণ অন্যরকম, ঘর তো নয়, যেন এক রাজ দরবার। কাঠের সিলিং-এর বিশাল ঝাড়বাতি, মেঝেতে মখমলের কার্পেট, ঘরময় আতরের তীব ঘ্রাণ-যেন এক সম্মোহনের রাজ্য। তিনি গিয়ে বসলেন ঝলমলে গালিচা বিছানো এক রাজকীয় খাটে। তাঁর ঠিক সামনে একটা বাক্স, ঠিক আড়তদারদের ক্যাশ বাক্সের মত। আমরা বসেছি বাক্সের ঠিক সামনে, পাশাপাশি দুটো চেয়ারে। খাটের পাশে রাখা সুদৃশ্য অ্যাকুয়ারিয়ামে শোভা পাচ্ছে বর্ণালি মাছের ঝাঁক। সাধারণ এক গ্রামের বাজারে এসব দেখে আমার রীতিমত ভিরমি যাওয়ার অবস্থা। আসলে এ হচ্ছে সাধারণ মানুষদের অন্যমনস্ক করার একটা কৌশল। তবে লোকটা যে এত দিনে অগাধ ক্ষমতার মালিক হয়ে গেছে তা এই ঘরের বিত্ত-বৈভব দেখেই বোঝা যায়। পোশাক আশাকে সুফী হলেও লোকটার ঘোলাটে চোখের দৃষ্টি ঠিক নেশাগ্রস্ত মানুষের মত।
বাবা এক সময় হাসতে হাসতে বললেন, আপনার কেরামতির অনেক গল্প শুনেছি, আজ নিজের চোখে দেখতে এলাম। তাঁর কথা শেষ হওয়ার প্রায় সাথে সাথেই লোকটা তাঁর খালি হাত বাবার সামনে মেলে ধরলেন, পরক্ষণেই সেটা মুষ্টিবদ্ধ করে নিজের মুখের সামনে এক পাক ঘুরিয়ে মেলে ধরলেন। তার হাতের তালুতে দেখা গেল ছোট সাইজের একটা ফুট কেক। তিনি আমার দিকে কেকটা এগিয়ে দিলেন। পরক্ষণেই তাঁর হাতে শোভা পেল আঙুরের আকৃতির কিছু টকটকে লাল ফল। আমার দিকে এগুলো এগিয়ে দেয়ার সময় তিনি বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, এ হচ্ছে অচিন ফল, জিন ছাড়া এই ফল আনার সাধ্য আর কারও নাই। কেকটা আমার খুবই চেনা, থানা সদরের বিভিন্ন কনফেকশনারী দোকানে পাঁচ টাকা দরে বিক্রি হয়। ফলগুলো চিনতে পারলাম না। একটা মুখে দিতেই মনে হলো এগুলো তাজা নয়। কোনও কিছু মিশিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষণ করা হয়েছে। আমি তখন প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। কিন্তু তিনি তেমন কিছুই করলেন না। আরও কিছুক্ষণ লোকটার সঙ্গে হাস্যরসাত্মক কথা বলে বাইরে বেরিয়ে এলেন। বাবার আচরণ আমাকে হতাশ করল, তিনি কি বুড়িয়ে যাচ্ছেন, নাকি আমাকে নতুন এক ভেলকিবাজির জগতের সঙ্গে পরিচয় করাতে এখানে নিয়ে এসেছিলেন? তবে কি অতীন্দ্রিয় জগতের সঙ্গে ভেলকিবাজির কোনও সম্পর্ক কিংবা যোগসূত্র আছে? এ নিয়ে কি নতুন করে কিছু ভাবছেন তিনি? জিজ্ঞেস করেও উত্তর পাওয়া গেল না। তবে আমি জানি এক সময় তিনি সবই আমার কাছে ব্যাখ্যা করবেন, সেটা দুদিন পরেও হতে পারে কিংবা দুবছর পর। বাবা এরকমই ছিলেন। সেদিন বিদায় নেয়ার আগে ওই লোকটা শূন্য থেকে একটা তাবিজ ধরে এনে আমায় দিয়েছিলেন, লেখাপড়ার উন্নতির জন্যে। তাবিজে কাজ হয়নি।
.
বছর খানেক পর এক সকালে খবর পেলাম টেকপাড়ার রাজ্জাক মিয়ার মেয়ের লাশ ঝুলে আছে বাড়ির অদূরে বাঁশ ঝাড়ের ভিতর। প্রায় দৌড়ে গেলাম ঘটনাস্থলে। দুর্ভেদ্য কাঁটাঝাড়ি বাঁশ ঝাড়ের ঠিক মাঝখানে মাটি থেকে প্রায় দশ ফুট উপরে গলায় শাড়ি পেঁচানো অবস্থায় ঝুলে আছে তরুণীর নিষ্প্রাণ দেহ। যেখানে মেয়েটা ঝুলে আছে তার চারদিক বাঁশ আর কঞ্চিতে ভরা, সেখানে তার পক্ষে তো দূরের কথা কোনও শক্ত-সমর্থ যুবকের পক্ষেও ওঠা সম্ভব নয়। কেউ যে তাকে হত্যা করে এমন জায়গায় নিয়ে ঝুলিয়ে রাখবে, সে চিন্তাও কারও মাথায় এল না। দুপুরের দিকে পুলিশ আসার পর বেশ কয়েকটা বাঁশ কেটে মেয়েটার লাশ নামিয়ে আনা হয়েছিল। সবাই তখন বলাবলি করছিল, এইটা হইতাছে চাড়াল জিনের কাজ, জিনের মধ্যে তারাই হইতাছে সবচাইতে বদ। এই ঘটনার উপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে রহস্যপত্রিকায় ফাল্গুনের আঁধার রাতে নামে একটি গল্পও লিখেছিলাম।
ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা শেষ হওয়ার কিছুদিন পরের কথা। আমাদের বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে মাসুম ভূইয়ার বাড়িতে এক মহিলা বেড়াতে এলেন। দুএক দিনের মধ্যে গ্রামময় রটে গেল মহিলার জিন সাধনার খবর। একের পর এক লোক আসতে লাগল মাসুমের বাড়িতে। একেকজনের একেকরকম সমস্যা। কারও মেয়েকে তাবিজ করে নষ্ট করেছে কেউ, কারও বাচ্চা হয় না, কারও বিয়ে হয় না, কেউ চাকরি পাচ্ছে না আবার কেউ বউ পাচ্ছে না-নানা ধরনের সমস্যায় জর্জরিত মানুষের ভিড় বাড়তে লাগল দিনে দিনে।
এক সকালে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে হাজির হলাম মাসুমের বাড়িতে। মাসুম আমার চাইতে বছর পাঁচেকের বড়, ওর বউকে ভাবী বলেই ডাকি। বাড়ির ভিতর ঢুকতেই পান্না ভাবী আমাকে দেখে কেমন যেন চমকে উঠলেন। মৃদু হেসে বললাম, আপনাদের মেহমানের সঙ্গে একটু দেখা করতে এসেছি। আর কিছু বলার আগেই ভাবী আমাকে জানালেন, এই মহিলা তার দূরসম্পর্কের খালা, বহু অনুরোধের পর এই প্রথমবারের মত তাঁদের বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন। তাঁর কথা আমার কাছে সত্যি বলে মনে হলো না। তিনি কিছুটা অপ্রস্তুত অবস্থায় আমাকে দক্ষিণের ভিটার ছোট্ট দোচালা ঘরে নিয়ে গেলেন।
চৌকির উপর বসে থাকা মহিলার বয়স নিঃসন্দেহে পঞ্চাশ পেরিয়েছে বছর কয়েক আগে। বয়সের সঙ্গে বেমানান রঙচঙে একটা শাড়ি পরেছেন তিনি, কাঁচা-পাকা চুল ছড়িয়ে আছে কাঁধের উপর। আমি ঘরে ঢুকতেই তিনি হেসে উঠে বললেন, কীয়ের লাইগ্যা আইছচ, ভাই, কী সমস্যা তোর?
কোনও রকম ভণিতা ছাড়া সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, আমি জিন বিশ্বাস করি না, আপনি যদি আমাকে জিন দেখাতে পারেন তবে বিশ্বাস করব।
আমার কথায় প্রথমে তিনি চমকে উঠলেন, পরক্ষণেই রেগে উঠে প্রায় চেঁচিয়ে বললেন, এই কতা আরও একজন কইছিল, জিনে আইস্যা তারে এমুন মাইর দিল, ছয় মাস হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে থাকতে হইছিল। আমার লগে যেইডা থাকে হেইডা হইল বদরাগী জিন; আমারেও মারে। এরপর তিনি আমার সামনে তার হাতের কব্জি আর পায়ের গোড়ালি মেলে ধরলেন, জায়গাগুলো স্বাভাবিকের চাইতে কিছুটা ফোলা। মহিলার বাতজ্বর থাকতে পারে। তাই এসব দেখে আমি মোটেও বিচলিত হলাম না। আর তাতে তিনি আরও খেপে গিয়ে আচমকা বলে উঠলেন, ওই দেখ কী বড় সাপ, চাইয়া দেখ, ভাল কইরা চাইয়া দেখ, বেশি তেরিবেরি করলে এই সাপে তরে খাইব। তাঁর দৃষ্টি ঘরের মেঝেতে। আমার পাশে বসা পান্না ভাবীও ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে আছেন। পান্না ভাবী যে সাপ দেখছেন তাতে কোনও ভুল নেই, ভয়ঙ্কর আতঙ্ক ভেসে আছে তার মুখে। শুনেছি এই মহিলা অনেককেই এভাবে সাপ দেখিয়েছেন।
কিন্তু আমি কিছুই দেখতে পেলাম না। সরাসরি সেটা না বলে বললাম, আমি সাপ ভয় পাই না।
বাকিটা পান্না ভাবীই খোলসা করলেন, ওনায় সাপ ধরে, সাপ নিয়া খেলা করে, শুনছি সাপের মাংসও খায়।
কথাগুলো শোনার পর মহিলার, চোখ দুটোতে কেমন এক শীতল আভা নেমে এল। তারপর ঠিক আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বললেন, ঠিক আছে, তোর যখন এতই শখ, আইজ রাইত বারোটায় আইবি।
মাসুমের বাড়ি থেকে বেরিয়ে মনটা কেমন যেন করে উঠল, এই ভেলকিবাজ মহিলার সঙ্গে লাগতে যাওয়া কি ঠিক হচ্ছে? আসলে আমার মধ্যে তখন একটা চিন্তাই কাজ করছিল, যে কোনও উপায়ে এই মহিলাকে এলাকা থেকে তাড়াতে হবে। বিপদগ্রস্ত মানুষের সরলতার সুযোগ নিয়ে। পানিপড়া, তিলপড়া, তাবিজ-কবচ, এসব দিয়ে মোটা টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন তিনি।
বিকেল পর্যন্ত বাড়িতে না গিয়ে বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা। বলে জেনে নিলাম ওই মহিলার উপর জিন ভর করলে তিনি কী ধরনের আচরণ করেন। আরও জেনে নিলাম সেখানে সমবেত লোকজন কীভাবে কথা বলে জিনের সঙ্গে। এসব জানার পর আমার ভিতরটা কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। কারণ যাদের সঙ্গে কথা হলো তাদের প্রায় সবারই বিশ্বাস, ওই মহিলা জিন ডেকে আনতে পারে। আরেকটা বিষয় খুবই অবাক লাগল, ওই সব লোকদের কয়েকজন আবার শিক্ষিত এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত।
রাত তখন ঠিক বারোটা। আমার সামনে আনকোরা কাপড় পরে মাথায় ঘোমটা দিয়ে তিনি বসে আছেন। নতুন শাড়ি না পরলে নাকি জিন বিরক্ত বোধ করে। আমাদের মাঝখানে পানিতে ভরা অ্যালিউমিনিয়ামের গোল পাত্র। লম্বা একটি বাঁশের কঞ্চি ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছে পাত্রের জল থেকে খোলা জানালা পর্যন্ত। মহিলা তখন একদম চুপ। কিছুক্ষণ আগেও তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি শান্তই ছিলেন। রাগারাগী করেননি কিংবা আমাকে ভয় দেখানোর চেষ্টাও করেননি। আসলে আমি নিজেই তখন কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিলাম। লোকজনের কাছে শুনেছি, তারা সবাই জিনকে হুজুর বলে সম্বোধন করে। মিনিট পাঁচেক অপেক্ষার পর নিজে থেকেই জিজ্ঞেস করলাম, হুজুর কি আসছেন? আমার ভিতরটা কেঁপে উঠল। জিনের সঙ্গে কথা বলা, এ তো কোনও সাধারণ বিষয় নয়! আমি সালাম জানিয়ে বললাম, হুজুর, আপনার আসতে এত দেরি হলো কেন?
সালামের উত্তর জানিয়ে জিন বলল, সিলেটের দরগায় জিকিরে
আছিলাম। কিছুটা নীরব সময় পেরিয়ে গেল। আসলে কেন জানি না আমি তখন কোনও প্রশ্ন বা কথা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তারপর এক সময় নীরবতা ভাঙল জিনের কণ্ঠ, তুই সাপ নিয়া খেলা করস, এই সাপের হাতেই তর মরণ হইব।
এমন কথার আকস্মিক ধাক্কায় প্রথমে ঘাবড়ে গেলেও পরক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম, হুজুর, যে সাপ নিয়ে খেলে সে মৃত্যুকে পরোয়া করে না।
তখন মহিলা আচমকা মাথার ঘোমটা সরিয়ে ফেললেন। আমি সোজা তাঁর চোখের দিকে তাকালাম। তিনি বললেন, এর কি জীবনের মায়া নাই।
খুব স্বাভাবিক গলায় উত্তর দিলাম, কে এই সুন্দর দুনিয়া ছেড়ে যেতে চায়?
তখন দ্রুত তার ডান হাতটি মাথার পেছন দিক থেকে ঘুরে এল। আমার সামনে মুঠি খুলে ধরতেই নীল পাথর বসানো একটি সোনার আংটি চোখে পড়ল। পরক্ষণেই তিনি আবার সেটাকে অদৃশ্য করে ফেললেন। বুঝতে মোটেই কষ্ট হলো না, তিনি চাইছেন আমি যেন তার কাছে আংটিটা দাবি। করি, বিপদ মুক্তির আশায়। আমার সাহস ফিরে এল। তার কথায় কিংবা চোখের ভাষায় মোটেও প্রকাশ পাচ্ছে না যে তার উপর কোনও কিছু ভর করেছে। একমাত্র হাতের কারসাজিই তার সম্বল। তখন হঠাৎ আমার দৃষ্টি চলে গেল। জানালার বাইরের আকাশে, আহা, কী সুন্দর চাঁদ! অবলীলায় আমার মুখ দিয়ে কথাগুলো বেরিয়ে এল, হুজুর, আপনারা তো আগুনের তৈরি, নিশ্চয় চাদে যেতে পারেন, আমায় চাঁদের গল্প বলুন।
আর ঠিক তখনই ওই মহিলা পাশে রাখা ঝাড়-ফুক করার ঝাড় নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। কঠিন চোখে তার দিকে তাকিয়ে বললাম, হুজুর, আপনি শান্ত হোন, আমি এখনই চলে যাব। মহিলা বসলেন আর আমি পকেটে হাত রাখলাম। কয়েকদিন আগে গ্রামের পথে হাঁটতে গিয়ে টেনিস বলের আকৃতির একটা লোহার বল কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। ওটা ইদানীং প্রায়ই আমার পকেটে থাকে, এখনও আছে। বলটা বের করে মহিলার হাতে দিলাম, ওজন দেখে তিনি মনে হয় কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন। তারপর ওটা তার কাছ থেকে আমার হাতে ফিরিয়ে এনে খুব ঠাণ্ডা গলায় বললাম, হুজুর, কাল যদি আপনি আসেন তা হলে এটা সোজা আপনার পেছন দিক দিয়ে ঢুকিয়ে দেব। কথাটা বলেই দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। পরদিন মাসুমের বাড়িতে গিয়ে কেউ আর মহিলার দেখা পেল না।
জিন নিয়ে ভাবনার যে জিন সদা আমার শরীর কোষে বিরাজমান, তা এসেছিল বাবার কাছ থেকে। কত কিছুই না জানার ছিল তার কাছে। আমার অনেক প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে আচমকা তিনি চলে গেলেন সেই মহাপ্রশ্নের না ফেরার দেশে। তাঁর মৃত্যু আমাকে এক বেপরোয়া জীবন এনে দিল। কারণ তিনিই ছিলেন আমার সবচেয়ে বড় ভালবাসা, সবচেয়ে বড় ভয়। থাক সে কথা। বাবার মৃত্যুর বছর চারেক পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে এক স্বাধীন জীবন বেছে নিলাম। এখন মনের সুখে ছবি তুলি, গল্প লিখি, ঘুরে বেড়াই নানান জায়গায়। মাঝে মধ্যে কিঞ্চিৎ মদ্যপান করি, মন্দ লাগে না। আর সাপের ভাবনা, জিনের চিন্তা এসব তো সঙ্গে আছেই।
এক সন্ধ্যার কথা। টেকপাড়ার রিকশা চালক ফালু দেখা করতে এল আমার সঙ্গে। তার মুখে গভীর বিষণ্ণতার ছাপ। সে বলল, ভাইজান, বড় বিপদের মধ্যে আছি, ছোড় মাইয়াড়ার উপর জিন ভর করছে আইজ আট দিন, আপনেরে নিতে আইছি।
ভিতরে ভিতরে উত্তেজিত হয়ে উঠলেও অবাক হওয়ার ভান করে বললাম, আমি গিয়ে কী করব, তুমি বরং কাদির মুন্সির কাছে যাও অথবা শুক্রবারে জেলা সদরে একজন ভাল মনোচিকিৎসক আসে, মেয়েকে নিয়ে তার কাছে যাও।
ফালু নাছোড়বান্দা। সে বার বার বলতে লাগল, আপনারে একবার যাইতেই হইব, আপনে গেলে একটা না একটা কিছু ঘটব।
সাপের চাউট্টা নিতে আসা বৃদ্ধের মত ফালুর মনেও হয়তো ধারণা, গোপনে আমি জিনের সাধনা করে থাকি। আসলে আমি ওখানে গেলে তেমন বিশেষ কিছু ঘটার সম্ভাবনা নেই, নিতান্ত একজন দর্শক ছাড়া আমি যে আর কিছুই নই। তবু ফালু যখন চাইছে আর আমার নিজেরও আগ্রহের কমতি নেই, তাই তাকে বললাম, ঠিক আছে, কাল বিকেলেই আমি তোমার বাড়িতে যাব।
গ্রামের দক্ষিণের টিলার মত উঁচু জায়গায় টেকপাড়ার অবস্থান। বিকেলের সোনারোদ মাথায় নিয়ে লাল মাটির পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে ফালুর বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বাড়িটার অবস্থান লোকালয় থেকে কিছুটা দূরে। চারদিকে বিশাল সব গাছপালা, বিশেষ করে বাড়ির দক্ষিণ দিকের প্রাচীন তালগাছের সারি চোখে পড়ার মত। একটা বিস্তৃত বাঁশ ঝাড়ও নজরে পড়ল। জায়গাটার নির্জনতা আমার মনে ধরল, একটা অতিপ্রাকৃত ভাব আছে বটে! এসব ভাবতে ভাবতে পা চালিয়ে বাড়ির সীমানায় ঢুকে পড়লাম, বিশাল বাগানের মাঝখানে ছোট্ট এক বাড়ি। আসলে এই গোটা সম্পত্তির মালিক রফিক ব্যাপারি, তিনি ফালুকে এখানে বাড়ি করে থাকতে দিয়েছেন জায়গাটা দেখশোনা করার জন্য।
ছোট্ট বাড়িটার ঝকঝকে উঠনে তখন কম করে হলেও পনেরোজন মহিলা অর্ধচন্দ্রাকারে বসে আছেন আর তাঁদের সামনে বারান্দায় বসে আছে বছর আষ্টেকের এক শিশুকন্যা। আমায় দেখে দৌড়ে এল ফালু। তার কাছ থেকে জানতে পারলাম, কিছুক্ষণ আগে মেয়েটার উপর জিন ভর করেছে। আরও জানলাম, এই জিন মানুষের অতীত ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারে, চিকিৎসা জানে নানা অসুখের। আমি খুব মনোযোগ দিয়ে মেয়েটার কার্যক্রম নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। তখন এক মহিলা জিনের উদ্দেশে নিজের সমস্যার কথা বলে চলেছেন, আইজ পাঁচ বছর হয় আমার স্বামী নিরুদ্দেশ, তাইনে কই আছে, দয়া কইরা আমারে কইয়া দেন।
মহিলার কথা শেষ হওয়ার প্রায় সাথে সাথে মেয়েটি বলল, তর জামাই মইরা গেছে দুই বছর আগে, হ্যায় আর ফিরা আইব না কোনওদিন।
এ কথা জানার পর মহিলা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। এরপর পাশের এক মহিলা দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ শ্বাসকষ্টে ভুগছেন, বহু ডাক্তার কবিরাজ দেখিয়েছেন কিন্তু কিছুতেই অসুখ ছাড়ছে না। মহিলার কথা শেষ হওয়ার পর মেয়েটা বসা থেকে উঠে হনহন করে উঠান পেরিয়ে বাড়ির পাশের ঝোঁপ-জঙ্গলে পূর্ণ বাঁশ ঝাড়ের ভিতর ঢুকে পড়ল। কিছুক্ষণ পর হাতে একটা গাছের শেকড় নিয়ে বেরিয়ে এল। তারপর মহিলার কাছে গিয়ে শেকড়টা এগিয়ে দিয়ে বলল, এই, শিকড় গরম সরিষার তেলে ডুবাইয়া রোজ রাতে বুকে মালিশ করবি, সব ঠিক হইয়া যাইব।
আমার সকল চিন্তা-চেতনা তখন বিস্ময়ের চূড়ায়। এতটুকু একটা মেয়ে, অথচ কী পরিপক্ক মানুষের মত আচরণ করে চলেছে! কী তার চাহনি! কী তার কথা বলার ধরন! সে বুড়ো মানুষের মত একের পর এক পান চিবিয়ে চলেছে, পানের রস গড়িয়ে পড়ছে তার চিবুকের দুপাশ বেয়ে। আরও একটা পান মুখে পুরে পানের বাটায় হাত দিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, ফালু, এই, ফালু, হাদা (তামাক পাতা) শেষ, তাড়াতাড়ি হাদা লইয়া আয়।
ফালু তখন আমার পাশ দিয়ে দৌড়ে পাশের ঘরে ঢুকল। তামাক পাতা হয়তো খুঁজে পাচ্ছিল না, তাই বেরিয়ে এল কিছুক্ষণ পর। তামাক পাতা হাতে তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে। মেয়েটার নাম মীম, এতক্ষণ মনে করতে পারছিলাম না। মীম হাতের ইশারায় তাকে ওর সামনে বসতে বলল। ফালু মাটিতে বসার সঙ্গে সঙ্গে মীম তার গালে সজোরে এক থাপ্পড় বসিয়ে বলল, হাদা আনতে এত দেরি হইল ক্যান, শয়তানের বাচ্চা?
ফালু কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আর এমুন হইব না, আমারে মাপ কইরা দেন।
তৎক্ষণাৎ আমি যেন বোবা হয়ে গেলাম, পরক্ষণেই বুঝলাম, ইদানীং এমন থাপ্পড় ফালুকে প্রায়ই খেতে হয়।
সন্ধ্যার একটু আগে উঠন ফাঁকা হয়ে গেল। আমি আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে তার সামনে বসলাম। এখানে আসার আগে বাজার থেকে কিছু চকলেট কিনেছিলাম। পকেট থেকে সেগুলো বের করে তার দিকে এগিয়ে দিলাম। চকলেটের দিকে এক পলক তাকিয়ে পরক্ষণেই সে তাকাল আমার চোখের দিকে। সে কী অন্তর্ভেদী দৃষ্টি! যেন আমার ভিতরটা পড়ে নিতে চাইছে। মিনিট খানেক এভাবে তাকিয়ে থাকার
হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে বলল, এই লোক এইখানে আইছে ক্যান, ফালু? হ্যারে বিদায় কর, নইলে এর সর্বনাশ হইব কইতাছি।
আমি তখন আরও সন্নিকটে গিয়ে মীমের বাম হাত ধরলাম। তারপর তার কড়ে আঙুলের নখের ঠিক নীচে নিজের বুড়ো আঙুলের নখ দিয়ে চাপ দিলাম (কৌশলটা কাদির মুন্সির কাছ থেকে শেখা।) মীম হাত ছাড়াতে ব্যস্ত হয়ে উঠে বলল, তুই চইল্লা যা, চইল্লা যা তুই।
বেশ স্বাভাবিক গলায় বললাম, আমি বেশিক্ষণ থাকব না, আমার কিছু প্রশ্নের উত্তর দিলেই চলে যাব। এই কথায় কিছুটা শান্ত হলো সে। জিজ্ঞেস করলাম, আপনার নাম কী?
সে ঠাণ্ডা গলায় বলল, আমার নাম ফাতেমা, তয় আমি একলা না, আমার লগে আরও একজন আছে।
জানতে চাইলাম, আপনারা কেন এর উপর ভর। করেছেন? মীম কিছু বলল না। কড়ে আঙুলে বুড়ো আঙুলের চাপ বাড়ালাম।
সাথে সাথে খেপে ওঠা গোখরোর মত ফোঁস ফোঁস করে বলল, বেশি কতা কইলে মাইয়াডারে মাইরা থুইয়া যামু।
আমি অনুনয়ের সুরে বললাম, দেখুন, মেয়েটা ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে আর বাড়ির মানুষগুলো খুব বিপদে আছে। দয়া করে আপনারা চলে যান।
মীম হাত ছাড়াতে ব্যস্ত হয়ে উঠল। তখন দূরের মসজিদ থেকে ভেসে এল মাগরিবের আযানের ধ্বনি। আমি ওর হাত ছেড়ে দেয়ার আগ মুহূর্তে বললাম, শুনেছি আপনারা এ বাড়ির সবাইকে নামাজ পড়তে বারণ করেছেন, আমি মাগরিবের নামাজ আদায় করে এখান থেকে যাব। মীমের হাত ছেড়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চেহারায় এক অস্বাভাবিক পরিবর্তন ভেসে উঠল, চোখ দুটি যেন কোটর ছেড়ে বেরিয়ে এল, গাড়ির পিস্টনের মত ওঠানামা করতে লাগল বুক। ফালু আমার পাশ থেকে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে মেয়েটার খুব কষ্ট হচ্ছে।
ফালু মেয়ের দেহটা বুকে চেপে ধরে বলল, ভাইজান, এইভাবেই জিকির দিয়া জিন আসে আবার জিকির উঠাইয়া চইল্লা যায়।
এরপর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই চেতনা হারিয়ে বাবার বুকে এলিয়ে পড়ে মীমের ছোট্ট দেহটি। আমি মাদুর বিছানো দাওয়ায় মাগরিবের নামাজ আদায় করতে দাঁড়িয়ে যাই।
নামাজ শেষ হওয়ার পর ফালু আমাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। হারিকেনের আলোয় দেখলাম, মীম তার পুতুলের বাক্স খুলে বসেছে। আমি গিয়ে পকেট থেকে চকলেটগুলো বের করে তার সামনে মেলে ধরলাম, সাথে সাথে লুফে নিল সে। নিষ্পাপ কোমল মুখটি খুশিতে ঝলমল করে উঠল। আমার কাছে তখন মনে হলো, এই দুনিয়া সত্যিই বড় রহস্যময়।
বিদায় নেয়ার আগে ফালুকে আমি আগের সিদ্ধান্তের কথাই জানালাম। হয় কাদির মুন্সি নয়তো মনোচিকিৎসক। আমি ওই দুজায়গাতেই এসব অসুস্থ মানুষদের অনেককে সুস্থ হতে দেখেছি।
মীমদের বাড়ি থেকে যখন বের হলাম তখন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নেমেছে। গ্রামীণ পথ ধরে কিছু দূর এগিয়ে আসার পর কী মনে করে পেছন দিকে তাকালাম। পরিষ্কার তারার আলোয় প্রাচীন গাছগুলোকে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়ানো দানবের মত লাগছিল। আমার তখন খুব কষ্ট হচ্ছিল এই ভেবে, কী গভীর আতঙ্কে ওই বাড়ির মানুষগুলোর রাত কাটে!
এ কাহিনি লেখার প্রথম দিকে যে কলাগাছটা ভেঙে পড়েছিল, পরদিন নদীতে নেমে ওটাকে কিনারায় টেনে তুলতেই রহস্যের সমাধান পাওয়া গেল। গাছের মাথায় আলিশান সাইজের ছড়া। গ্যাড়া সুন্দর জাতের কলার ছড়া যেমন বড় হয় গাছও তেমনি বিশাল। ছড়ার ভারেই বিরাট কলাগাছটি নদীতে ভেঙে পড়েছিল। তবে কথা হচ্ছে-গাছ ভাঙার আর সময় ছিল না?
পিপাসার্ত – তানজীম রহমান
শেষ একটা টান দিয়ে সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল এখলাস মুয়াজ্জিন।
যে বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এধরনের বিরাট আলিশান বাড়িতে ওর শ্রেণীর লোকজন শুধু একটা কারণেই আসে। তৈলাক্ত হাসি মুখ নিয়ে ধনী মালিকদের কাছে সাহায্য চাইতে। স্যর, আমার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দেন, স্যর, আপনারাই মা-বাপ। স্যর, যদি কিছু দিতে পারেন তা হলে বাচ্চাটা পরের ক্লাস পড়তে পারবে, স্যর, নইলে এত ভাল।
একটা ছাত্রের ভবিষ্যৎ এখানেই শেষ, স্যর।। কিন্তু এখলাস মুয়াজ্জিন এখানে সাহায্য চাইতে আসেনি, বরং বাড়ির মালিক ডেকে এনেছে। একটা ব্যাপারে তার সাহায্য দরকার। এমন একটা ব্যাপারে যেটায় এখলাস ছাড়া। আর কেউ কিছু করতে পারবে না।
নিজের সন্তুষ্ট হাসি গোপন করবার কোনওরকম চেষ্টা না করে এখলাস মুয়াজ্জিন দরজার বেল বাজাল।
একজন বয়স্ক কাজের লোক এসে দরজা খুলে দিল। আসেন, হুজুর, আমার পিছনে আসেন। বাধ্য ছেলের মত এখলাস তার পিছে পিছে একটা বিশাল বসার ঘরে এসে পৌঁছাল। ও এতক্ষণ ইচ্ছা করেই আশপাশে তাকিয়ে দেখেনি, যাতে চাকরটা মনে না করে যে এরকম বড়লোকের বাসায় ওর আগমন এই প্রথম।
কিন্তু ড্রয়িংরুমটায় এসে চোখ বড় বড় হয়ে গেল। এত সুন্দর রুম ও কখনও দেখেনি।
প্রকাণ্ড ঘরটার সবকিছু সাদা রঙ করা, মেঝে, দেয়াল, ছাদ, সবকিছু। দেয়ালে কয়েকটা ছবি টাঙানো, কিন্তু কোনও ফোটো নেই। গোলাকার মেঝের মাঝখানে একটা মাঝারি সাইজের পাথরের টেবিল রাখা, এটাও সাদা রঙের। আর টেবিলের চারপাশ ঘিরে পুরনো আমলের রাজকীয় চেয়ার রাখা, যেগুলোর মধ্যে একটায় ঢোলা, সাদা শার্ট আর জিন্সের পান্ট পরা শীর্ণ, ফর্সা এক যুবক বসে আছে। ছেলেটার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ আর বেপরোয়া।
এখলাসকে দেখে উঠে দাঁড়াল। এখলাস মনে মনে খুশি হলো। বড়লোক হলেও ছোকরা বেয়াদব নয়।
আসোলামু ওয়ালাইকুম। এখলাস বলল।
ছেলেটা সালামের জবাব না দিয়ে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিল। আপনি এখলাস মুয়াজ্জিন, তাই না? আসার জন্যে ধন্যবাদ। আপনাকে কি কালাম সাহেব জানিয়েছেন। আমার সমস্যাটা কী?
কালাম জোয়ারদার হচ্ছে এখানকার মসজিদের ইমাম। সে-ই এখলাসকে বলে এখানে আসতে। এখলাস ছেলেটার সাথে করমর্দন করে জবাব দিল, খুব বেশি কিছু নয়। উনি শুধু বললেন যে আপনার বাড়ির ওপর আসর হয়েছে, আর স্থানীয় হুজুররা কেউই কিছু করতে পারছেন না।
ছেলেটা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, এভাবে বললে। ব্যাপারটা কত তুচ্ছ মনে হয়, তাই না? হাত দিয়ে এখলাসকে ইঙ্গিত করল বসতে, নিজেও মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে পড়ল।
আপনি যদি সবকিছু খুলে বলেন তা হলে আপনাকে সাহায্য করতে আমার সুবিধা হবে। এখলাসের মতামত।
অবশ্যই, অবশ্যই, এজন্যেই তো আপনাকে এখানে আনা…মুরাদচাচা, অতিথি আপ্যায়নের বন্দোবস্ত করেন।
হুকুমটা শোনামাত্র বয়স্ক ভৃত্যটি মাথা নিচু করে সম্মতি জানিয়ে গায়েব হয়ে গেল।
ছেলেটা নিষ্প্রাণ, ফ্যাকাসে গলায় নিজের গল্প শুরু করল:
এখলাস সাহেব, আমার নাম হচ্ছে জামিল। জামিল সামাদ। এটা আপনি কালাম সাহেবের কাছ থেকে শুনে। থাকবেন। আমার বাবা ছিলেন এহসান সামাদ, ঢাকার প্রখ্যাত ধনীদের মধ্যে একজন। বড়াই করছি না, যাতে আপনি সবকিছু পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারেন তাই বলছি। ছেলেটা একটু থামল। এখলাসের মনে হলো ছেলেটা এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না পুরো গল্পটা বলবে কিনা। জামিল দম নিয়ে আবার শুরু করল, বাংলাদেশের অন্যান্য বড় ধনী ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্টদের মত বাবাকেও সম্পত্তির সিঁড়ি বেয়ে উঠবার সময় অনেক নোংরা কাজ করতে হয়েছে। তার ফল। হয়েছে এই যে মৃত্যুর সময় ওঁর সাথে কেউ ছিল না। মা আর বাবার অনেক আগেই ডিভোর্স হয়ে গিয়েছে, আর বছর দুয়েক আগে আমি বাবার অনুমতি না নিয়েই বিদেশে চলে যাই। বাবা এই ব্যাপারটায় প্রচণ্ড রাগ করেন। উনি আমার সাথে সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করে দেন। শুধু তাই নয়, উনি এই বাসায় আমার যত চিহ্ন ছিল সব নষ্ট করে দেবার চেষ্টা করেন। আমার ঘরের আসবাবপত্র, আমার ছবি সব পুড়িয়ে ফেলা হয়। এমনকী সেলিমচাচা নামে আমাদের একজন পুরনো, বিশ্বস্ত কাজের লোক ছিল, যে আমাকে ছোটবেলা থেকে লালন-পালন করেছে, তাকে বাবা বাড়ি থেকে বের করে দেন আমি চলে যাবার পর। তারপরও গত মাসে তার। মৃত্যুর খবর পেয়ে আমি আবার দেশে ছুটে আসি। আমার জেদ আর রাগের সাথে পরিচিত বলে কোনও আত্মীয়স্বজন আমাকে বাবার অসুস্থতার কথা জানায়নি। আমার ভিসা নিয়ে একটু ঝামেলা হয়েছিল, আর এসে দেখি বাবার কবর দেয়া হয়ে গেছে।
মুরাদ একটা ট্রে হাতে নিয়ে ঘরে ঢোকাতে জামিলের কথায় বাধা পড়ল। সে ট্রে থেকে টেবিলে বিস্কিট আর কেকের প্লেট নামিয়ে রাখল। আর এক কাপ চা।
এখলাস একটা কেক হাতে নেবার পর জামিল আবার শুরু করল, এখলাস সাহেব, যতই রাগ করে থাকি, উনি আমার বাবা। মরার আগে একবার ওর সাথে কথাও বলতে। পারলাম না, আর আমি ওঁর চেহারা দেখতে চাই না এ ধারণা নিয়েই উনি মারা গেলেন-এ ব্যাপারটা আমার সহ্য হয়নি। তাই আমি ওঁর সাথে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা নিই।
এখলাসের বিস্মিত দৃষ্টির জন্যে জামিল তৈরি ছিল। না থেমে বলে যেতে লাগল, আমি একজন শিক্ষিত মানুষ, এখলাস সাহেব। কিন্তু পাশাপাশি আমি একজন স্পিরিচুয়াল। মানুষও। আমি মানবাত্মার ব্যাপারে প্রচুর পড়াশোনা করেছি। আমি কোনও নির্দিষ্ট ধর্মে বিশ্বাস না করলেও এটা বিশ্বাস করি যে মানুষের স্থূল দেহের ভিতর এক ধরনের সূক্ষ্ম দেহ আছে, যার সাথে কিছু নিয়ম, কিছু পদক্ষেপ পালনের মধ্য দিয়ে যোগাযোগ করা সম্ভব।
ছোকরা তা হলে কাফির? তারচেয়েও খারাপ, এ তো মুশরিক বলে মনে হচ্ছে, যে কালো জাদুতে বিশ্বাস করে।
তা ছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে। আমার বাবার মৃত্যু খুব একটা স্বাভাবিকভাবে হয়নি। ওঁর অসুখ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সাধারণ অসুখ নয়।
কী তা হলে?
জলাতঙ্ক।
এখলাস কী বলবে বুঝতে পারছিল না।
সাধারণ নয় এ কারণে বলছি যে, বাবা কুকুর একদম পছন্দ করতেন না, এবং আমার জানামতে গত দশ বছরে বাবা কোনও কুকুরের কাছেও ঘেঁষেননি। ডাক্তারও বাবার মৃতদেহ পরীক্ষা করে বলেছেন যে তাঁর শরীরে কোনও কামড়ের দাগ নেই। কিন্তু মৃত্যুর আগে টানা তিন দিন বাবা পানি খাননি, জোর করে খাওয়াতে গেলে বমি করে বের করে দিয়েছেন, ইঞ্জেকশন দিতে গেলে এমন দাপাদাপি করেছেন। যে ডাক্তাররা কাছে আসতে পারেননি।
জামিল আবার একটু থামল। ওকে এখন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। আমি ঢাকায় আসবার পরের দিন রাতেই বাবার সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করি। কিন্তু কোনওরকমের সাড়া পাইনি। ঘণ্টা দুয়েক বসে থাকার পরেও মোমবাতির আলো পর্যন্ত নড়েনি। আমি ভেবেছিলাম বাবা হয়তো আমার সাথে কথা বলতে চান না। কিন্তু ঘটনা ঘটা শুরু করে তার পরের রাত থেকে।
এখলাসের মনে হলো ছেলেটার ঠাণ্ডা দৃষ্টিতে অন্য কীসের যেন ছাপ পড়েছে। ভয়?
সেদিন রাতে খাবার সময় পানি মুখে দেবার সাথে সাথে আমার বমি এসে পড়ে। পানিতে বিশ্রী, সোঁদা গন্ধ। প্রথমে ভেবেছিলাম জগে হয়তো ফাঙ্গাস পড়েছে, বা পানির ফিল্টারে। কিন্তু চেক করে কিছুই পেলাম না। আমি আর মুরাদচাচা মিলে ছাদের ট্যাঙ্কও দেখলাম, কিন্তু সেখানেও কোনও সমস্যা নেই। শেষ পর্যন্ত মুরাদচাচাকে বললাম দোকান থেকে মিনারেল ওয়াটার কিনে আনতে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার কি, জানেন?
এখলাস বুঝতে পারছিল ছেলেটা কী বলবে, কিন্তু তারপরও জিজ্ঞেস করল, কী?
দোকানের পানিতেও ঠিক একই গন্ধ! আর গন্ধটা এতই তীব্র যে সে পানি ঠোঁটে ছোঁয়ানোই কঠিন, খাওয়া তো দূরের কথা। সেদিন থেকে শুরু। তারপর থেকে প্রত্যেকদিন একই ব্যাপার। যে পানি খেতে যাই তারই একই অবস্থা। ডাক্তার দেখালাম, কোনও অসুখ ধরা পড়ল না। তা ছাড়া মুরাদচাচা তো একই পানি খাচ্ছেন, ওঁর তো কোনও সমস্যা হচ্ছে না। প্লাম্বার ডেকে পানির পাইপ চেক করালাম, বলা বাহুল্য, কিছুই ধরা পড়ল না। আর ব্যাপারটা আরও সঙ্গীন হয়ে দাঁড়াল তার পরের রাত থেকে। আমার বাসার প্রত্যেকটা কল থেকে পানি পড়া বন্ধ হয়ে গেল।
এখলাস এবার একটু থমকাল। এটা ও আশা করেনি।
আবারও বলছি এখলাস সাহেব, দম্ভ করছি না, কিন্তু বাবার এখানে প্রচণ্ড প্রতিপত্তি ছিল। আমি যখন এ বাসার নাম্বার থেকে ওয়াসার অফিসে ফোন দিই তখন ওদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় কে এসে পাইপ ঠিক করবে তা নিয়ে। কিন্তু ওরা এসে কোনও সমস্যাই খুঁজে পেল না। না আমার বাসার পাইপিং-এ, না ওদের নিজেদেরগুলোতে।
এখলাসের দিকে তাকাল জামিল।
কোনও সন্দেহ নেই, ছেলেটার চোখজুড়ে ক্লান্তি আর ভয়ের ছাপ পড়েছে।
. গত চার দিন ধরে আমি কোক আর জুস খেয়ে বেঁচে আছি। বাড়ির কাজের পানি বাইরে থেকে নিয়ে আসতে হয়। আমি বুঝতে পারছিলাম না যে বাবার আত্মা আমার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছে নাকি আমি অন্য কিছুকে ডেকে এনেছি। অতিষ্ঠ হয়ে আমি কালাম সাহেবকে খবর দিই। উনি বাড়িতে এসেই ঘাবড়ে যান। বারবার বলতে থাকেন যে এখানে খুব খারাপ কিছু হয়েছে। উনি কোনও অশুভ অস্তিত্ব অনুভব করছেন। উনি আমাকে বলেন যে এসব ব্যাপারে ওঁর তেমন কোনও অভিজ্ঞতা নেই। উনি আপনার কথা বলেন, বলেন যে কারও যদি এই সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা থাকে তা হলে আপনারই থাকবে। এখন বলেন, এখলাস সাহেব, শুনে আপনার কী মনে হয়? সুরাহা করা কি সম্ভব?
এখলাস চিন্তিত মুখে নিৰ্জের দাড়িতে হাত বুলাল।
দেখেন, জামিল সাহেব, এর আগে আমাকে জিনের আসর হওয়া দুটো বাসায় ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। আল্লাহপাকের দয়ায় ওদের সমস্যাগুলো কিছুদিনের মধ্যেই চলে গেছে। কিন্তু আপনার মত কেস ওদের কারওই ছিল না।
এখলাস একটা কুটিল হাসি গোপন করল। এদেরকে যত টেনশনে রাখা যায় টাকার অঙ্ক ততই বাড়ে।
তাই আমি এখনও বুঝতে পারছি না যে এখানে আমি কতদূর কী করতে পারব।
উত্তর দেবার সময় জামিলের চোখ উদ্বিগ্ন দেখালেও গলা। ঠাণ্ডাই রইল। আপনার যদি টাকা পয়সা নিয়ে কোনও চিন্তা থেকে থাকে তা হলে তা দূর করে দিন। আমার এই সমস্যাটা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমাধান করতে হবে, ঠিক আছে? যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ওর গলা শেষের দিকে কঠিন শোনাল।
এখলাস ভিতরে ভিতরে একটু অবাক হলো। জামিল আসলেই ভয় পেয়েছে। ভীষণ ভয়। ওকে দেখে সহজে ভয় পাবার ছেলে বলে মনে হয় না।
আমি আজ সকাল থেকে জুসও খেতে পারছি না, এখলাস সাহেব, জামিলের গলা ক্লান্ত, ভেঙে পড়া একজন মানুষের গলায় পরিণত হলো। ফলের রস, কোল্ড ড্রিঙ্কস্, যাই খেতে যাই না কেন, ওই অসহ্য গন্ধটা আমার নাকে এসে লাগে। আপনি যদি কিছু না করতে পারেন আমিও বাবার মত পানির পিপাসায় মারা যাব।
.
সেদিন রাতে এখলাস শোবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। সে জামিলকে কথা দিয়ে এসেছে কালকেই জামিলের বাড়ি দোয়া পড়ে বন্ধ করে দিয়ে আসবে। সাধারণত এটা করতে পাঁচজন লাগে, তাই এখলাস আগামীকাল ওর দুই সাগরেদকে নিয়ে যাবে।
বিছানায় মশারি খাঁটিয়ে শুয়ে পড়ল। মগবাজারের একটা। ছোট বাসায় থাকে। বিয়ে-থা করেনি, এখানে থাকতে ওর তেমন সমস্যা হয় না। পুরনো বাসা, তাই হাজারো সমস্যা। মাঝে মাঝে ওর শোবার ঘরের লাইট নিজে থেকেই কয়েক ঘণ্টার জন্যে বন্ধ হয়ে যায়, আর বাথরুমের কল থেকে নিরন্তর টিপ টিপ পানি পড়তে থাকে, কিন্তু এখলাস কখনোই এসব নিয়ে বেশি মাথা ঘামায়নি।
এখলাস বেশি রাত জাগে না। আজকেও বিছানায় শুয়ে রাতের শব্দ শুনতে শুনতে ওর চোখ বুজে এল ঘুমে। জানালার বাইরে থেকে একটা নিশাচর পাখির কর্কশ ডাক ভেসে আসছে। দেয়ালে টিকটিকির টিক টিক ডাক। ফ্যানের ছন্দময়, যান্ত্রিক সঙ্গীত।
হঠাৎ ওর চোখ খুলে গেল। কী ব্যাপার? কী যেন মিলছে না। কোথায় যেন কী নেই। বিছানায় উঠে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করল কীসের অভাব অনুভব করছে।
পাঁচ মিনিট কেটে গেল। এখলাসের চোখে কিছুই ধরা পড়ল না। আবার শুতে যাবে তখন বিদ্যুৎচমকের মত বুঝতে পারল কোন্ জিনিসটায় ওর অস্বস্তি হচ্ছে।
বাথরুমের কল থেকে পানি পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে।
এখলাস গত দুই বছর ধরে এ বাসায় থাকছে, আর প্রত্যেক রাতে ওর নিদ্রার সঙ্গী ছিল কল থেকে টিপ টিপ পানি পড়ার ওই শব্দটা। কিন্তু আজকে শব্দটা আসছে না।
জামিল না বলেছিল ওর বাসার কলগুলো থেকেও পানি পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছে?
এখলাস বিছানা থেকে নেমে দাঁড়াল। দ্রুত পায়ে হেঁটে গিয়ে বাথরুমের লাইটটা জ্বেলে দিল। কিছুই নেই।
সত্যি বলতে কী, আশাও করেনি যে কিছু দেখবে। কিন্তু রাতের পরিবেশটাই এমন। কল্পনা অতি সাধারণ কোন ঘটনাকেও অলৌকিক রূপ দিতে চায়।
বাথরুমে ঢুকে দেখল কোথাও অস্বাভাবিক কিছু আছে। কিনা। ছাদের এক কোনায় একটা বিশাল, গর্ভবতী মাকড়সা ছাড়া চোখে পড়ার মত আর কিছু নেই। কলটা ছাড়তে পানির একটা ক্ষীণ ধারা পড়তে লাগল। সবই ঠিক আছে। লাইটটা নিভিয়ে বিছানায় ফিরতে যাবে এমন সময় জিনিসটা ওর চোখে পড়ল।
ওর মশারির ভিতর কী যেন বসে আছে।
অন্ধকারে একজন মানুষের আবছা আকৃতি দেখা যাচ্ছে। মানুষটা গুটিসুটি হয়ে বসে আছে, দুই হাঁটু বুকের সাথে জড়িয়ে। কপাল হাঁটু দুটোর ওপর রাখা। অসম্ভব শীর্ণ একজন মানুষ।
এখলাস এক কদম এগিয়ে এল।
মানুষটা নড়ল না। কিন্তু এখলাসের গলা থেকে একটা জান্তব গর্জন বেরিয়ে এল। গলাটা অপার্থিব, ভয়ঙ্কর। অনেকক্ষণ চিৎকার করবার পর মানুষের গলা যেমন ভেঙে ফাসফেঁসে হয়ে যায়, অনেকটা সেরকম।
এখলাস বিড়বিড় করে দরুদ পড়তে শুরু করল।
মটমট করে শব্দ হলো। মানুষটা আস্তে আস্তে মাথা তুলছে। ওর হাড়গুলো যেন অনেক পুরনো, ওর শরীরের ভার আর বহন করতে পারছে না।
এখলাস এবার জোরে জোরে দরুদ পড়তে লাগল। ওর কপালে চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে। আস্তে আস্তে বেডরুমের লাইটের সুইচটার দিকে এগোচ্ছিল।
মানুষটার মাথা আস্তে আস্তে এখলাসের দিকে ঘুরল।
দড়াম দড়াম করে প্রচণ্ড জোরে শব্দ হলো দরজায়। একটা গলা ভেসে এল বাইরে থেকে, হুজুর? সব ঠিক আছে। তো?
এখলাসও ঠিক সেই মুহূর্তেই লাইটটা জ্বেলে দিল। কিছুই নেই বিছানায়।
উঁচু গলায় প্রতিবেশীকে বলল, জি, কাদের সাহেব, সব ঠিকই আছে।
.
পরদিন এশার আযানের আগে আগে এখলাস ওর সাগরেদ কলিম আর রাশেদকে নিয়ে জামিলের বাড়িতে হাজির হলো। অল্প কথায় জামিল আর মুরাদকে বুঝিয়ে দিল কী করতে হবে। জামিল বাড়ির কেন্দ্রবিন্দুতে দাঁড়িয়ে আযান দেবে, সে। সময় এখলাস, কলিম, রাশেদ আর মুরাদ বাড়ির চারকোনায় সুরা পড়ে একটা করে পেরেক ঠুকবে। এতে ঘরের মধ্যে যদি কোনও অশুভ প্রভাব থেকেও থাকে, সেটার আর কারও ক্ষতি করবার ক্ষমতা থাকবে না।
গতকাল রাতে কী হয়েছে সেটা এখলাস জামিলকে বলেনি। যদি ছোকরা মনে করে যে হুজুর নিজেই ভয় পাচ্ছে। তা হলে এখলাসের বদলে অন্য কাউকে নিয়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। আর তা হলেই এতগুলো টাকা গচ্চা।
এখলাস সবাইকে ওজু করে নিতে বলে নিজেও বাথরুমে ঢুকল। এবং ঢুকেই একবার সাবধানে আশপাশে তাকাল না, কিছু নেই। পানিভরা বালতির পাশে বসে ওজু সেরে নিল।
ড্রয়িংরুমে এসে আরেকবার সবাইকে বুঝিয়ে দিল কী করতে হবে। তারপর একটা হাতুড়ি আর পেরেক হাতে নিয়ে চলে গেল বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। কলিম, রাশেদ আর মুরাদ বাকি তিন কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। আর জামিল দাঁড়াল ড্রয়িংরুমের মাঝখানে। এটাই বাসার কেন্দ্রবিন্দু।
জামিল শুরু করল: আল্লাহু আকবর আল্লাহু আকবর…
এখলাসও মনে মনে সুরা পড়তে লাগল। পেরেকের মাথাটা দেয়ালের সাথে চুঁইয়ে নিজেকে প্রস্তুত করল, যাতে জামিলের আযান শেষ হবার সাথে সাথে পেরেকটা ঠুকে দিতে পারে।
আসসাদু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ…
হঠাৎ এখলাসের কেমন যেন অস্বস্তি লাগতে শুরু করল। ওর গলা শুকিয়ে গেছে। ভয়ে নয়, বরং মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ পানি খায়নি।
জামিলের আযান থেমে গেল।
এখলাস হাতুড়ি-পেরেক ফেলে দৌড় দিল ড্রয়িংরুমের দিকে। বাড়িটা এত বড় যে দৌড়ে আসতে আসতেও প্রায় ৩০ সেকেণ্ডের মত লেগে গেল। হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পা দিল ড্রয়িংরুমের দরজায়।
আর সাথে সাথে বাড়ির সবগুলো আলো নিভে গেল।
এখলাস দেয়ালে হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে এল ঘরটার মাঝখানে, যেখানে জামিল দাঁড়িয়ে ছিল। সারা ঘর একটা অদ্ভুত, গা-শিউরানো শব্দে ভরে গেছে। একটা জান্তব, ফাসফেঁসে গলার গর্জন, ঠিক যেমন এখলাস, গতকাল রাতে শুনেছিল।
ঘরের মাঝখানে আসতে পায়ে কীসের সাথে যেন ধাক্কা খেল। সাথে সাথে ভয়ে স্থির হয়ে গেল এখলাস। নিচে তাকাবারও সাহস পেল না।
অন্য তিনজনও ততক্ষণে ড্রয়িংরুমে ছুটে এসেছে। তাদের মধ্যে একজনের হাতে একটা টর্চলাইট। সে আলোটা এখলাসের ওপর ফেলল। একমুহূর্তের জন্যে এখলাসের মনে হলো তীব্র আলোতে ওর চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। তারপর ওর চোখ চলে গেল মেঝেতে।
যে মানুষটা মেঝেতে শুয়ে আছে তাকে দেখে আর জামিল বলে চেনা যায় না। ওর শরীর শুকিয়ে কঙ্কালসার হয়ে গেছে, গায়ের চামড়া হয়ে গেছে রুক্ষ, খসখসে। ওর ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছে। কথা বলার চেষ্টা করছে, আর গলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে অর্থহীন, ফাসফেঁসে শব্দ। ওর চোখে তীব্র, অসহায় আতঙ্ক।
টর্চ হাতে মানুষটা ডুকরে কেঁদে উঠল। মুরাদ। জামিলচাচা! আপনের কী হইল! ইয়া আল্লাহ!
এখলাস কোনওমতে নিজেকে শান্ত করে আয়াতুল কুরসী পড়তে লাগল। কলিম আর রাশেদও কাঁপা কাঁপা গলায় যোগ দিল ওর সাথে।
জামিল শেষ একবার চিৎকার করে উঠল, তারপর স্থির হয়ে পড়ে রইল মাটিতে।
বাসার সবগুলো লাইট আবার জ্বলে উঠল।
.
এক মাস পর।
এখলাস নিজের বিছানায় শুয়ে পড়ল। ঘুমাবার আগে ওর মাথায় আরেকবার ভেসে উঠল সেই কালো দিনের ঘটনাগুলো। প্রায় প্রতি রাতেই ওর মনে পড়ে যায় জামিলের ভয়ঙ্কর, অসহায় চেহারা। ওর, চোখের ভয়। আর মুরাদের স্বীকারোক্তি।
জামিলের মৃত্যুর পর স্বভাবতই পুলিশ আসে। এসে সবাইকে সন্দেহভাজন হিসাবে জেরা করা শুরু করে। মুরাদ এমনিতেই ভেঙে পড়েছিল, পুলিশি জেরার সামনে আর নিজেকে সামলে রাখতে পারেনি। সব সত্য স্বীকার করে।
ওই বাড়িতে আরেকজন কাজের লোক ছিল, সেলিম, যে পেলে বড় করেছে জামিলকে, তাকে আসলে জামিলের বাবা বের করে দেননি। ছেলে না জানিয়ে বিদেশ চলে যাবার পর জামিলের বাবা রাগে উন্মাদ হয়ে যান। জামিলের সব জিনিসে আগুন ধরিয়ে দেবার পর তার চোখ পড়ে সেলিমের ওপর। উনি সেলিমকে নিয়ে হাত-পা বেঁধে বাসার নিচের একটা ঘরে আটকে রাখেন। তাকে কোনও খাদ্য-পানীয় কিছু দেয়া। হয়নি। মুরাদও তখন ভয়ে কিছু বলতে পারেনি। তিন দিনের মাথায় সেলিম পানির পিপাসায় মারা যায়। মুরাদ ওর লাশ গভীর রাতে একটা ডোবায় ফেলে দিয়ে আসে। মারা যাবার আগে সেলিমও নাকি শুকিয়ে অস্থি-চর্মসার হয়ে গিয়েছিল।
এটুকু বলেই মুরাদ কান্নায় ভেঙে পড়ে। ও বিলাপ করতে থাকে যে, সেলিমের আত্মাই প্রতিশোধ নিয়েছে জামিল আর ওর বাবার ওপর। ও হয়তো প্রথমে জামিলের ক্ষতি করতে চায়নি, কিন্তু জামিল নিজের বাবার আত্মার সাথে যোগাযোগ করতে চাওয়ার পর জামিলের ওপর রেগে যায়।
এখলাসের চোখে আলো পড়াতে পাশ ফিরে শুলো। এখন সারারাত বাথরুমের আলো জ্বেলে রাখে।
সাদা চোখ – সোহানা রহমান
খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেলে এমন হয়। মনটা কেমন জানি তরল থাকে। অজানা দুঃখে মন ভারী হয়ে থাকে। আবার অদ্ভুত ভাল লাগায় হৃদয় অবশ হয়ে আসে। কোথায় দূরে কুহু-কুহু করে একটা কোকিল ডাকছে। ভোরের বেলায় মনটা কেমন করে উঠল। জায়গাটা প্রথমে ভাল লাগেনি একটুও। কিন্তু জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বিস্তর ফসলের খেত আর সোনালি হয়ে ঝুঁকে পড়া ধান দেখতে-দেখতে খারাপ লাগা খুব বেশিক্ষণ থাকল না। রাতে ভাল ঘুম হয়নি। একে তো নতুন জায়গা। তার উপর সারারাত ট্রেইন চলে। কুউউউউউউউ করে হুইসেল বাজিয়ে মাঝে-মাঝেই ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছে। ভাইয়া এখানকার টি.এন.ও হয়ে এসেছে। বিশাল সরকারি বাংলো। অনেকগুলো রুম, কিন্তু থাকার মানুষ নেই। আমার পরীক্ষা শেষ বলে আমাকেই আসতে হয়েছে সংসার গুছিয়ে দেয়ার জন্য।
কাল অনেক রাতে ট্রেইনে করে আমরা পৌঁছেছি এখানে। তখন আর গুছানোর সময় ছিল না। তাই আমি একটা বেডরুমে আর ভাইয়া ড্রইংরুমে বিছানা করে শুয়ে পড়েছিলাম। আজ খুব সকালে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। কুয়াশায়। ঝাপসা হয়ে যাওয়া ধানখেতগুলোতে সেই ভোরেই কৃষকরা কাজ করছিল। ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরাও কাজ করছিল, কেউবা ব্যাগ কাঁধে করে স্কুলের উদ্দেশে রওনা করেছিল। সবকিছু এত ভাল লাগছিল যে আমি উঠে অনেকদূর হেঁটে এসেছিলাম। শিশিরে পা ভিজে উঠছিল, খোলা চুলে হাত দিয়ে মনে হয়েছিল কে যেন ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ভিজিয়ে দিয়েছে। অনেকক্ষণ ঘুরে যখন বাসায় ফিরলাম ভাইয়া তখন উঠে পড়েছে। আজই তার জয়েনিং-এর ডেট। রাস্তার পাশ থেকে গরম-গরম চা আর তেল চুপচুপে পরোটা কিনে এনে তাই দিয়েই নাস্তা হলো। ভাইয়া চলে গেলে আমি গোছগাছ শুরু করলাম। অল্প কটা জিনিস ভাইয়ার। তাই গুছাতে খুব বেশি সময় লাগল না। তারপর অফুরন্ত সময়। না আছে। টেলিভিশন, না আছে ইন্টারনেট
সময় কাটছিল না একটুও। অদ্ভুত এক জায়গায় বাংলোটা। আশপাশে কোন বাসা নেই। পিছনের দিকে বিস্তৃত ধানখেত, সামনের দিকে ট্রেইন লাইন। সেই ট্রেইন লাইন ছাড়িয়ে অনেকদূর গেলে মূল শহর। এই সৃষ্টিছাড়া জায়গায় কেন এত বড় একটা বাড়ি বানিয়েছিল কে জানে! পরিত্যক্ত সব বাড়ি সরকারি হয়ে যায়, পরবর্তীতে তা রূপান্তরিত হয় বাসভবনে। সেরকমই একটা বাড়ি এটা। কেউ থাকতে চায় না এই জনবিরল জায়গায়। এই বাড়িটা বুঝি ভেঙেই ফেলা হবে। নতুন সরকারি ভবন বানানো হচ্ছে, আর একমাসের ভিতর উঠে যাওয়া যাবে। ততদিন এই বাড়িতে থাকতে হবে। আর আমার ছুটি চলছে বলে এই একমাস আমিও ভাইয়ার সঙ্গে এইখানে থাকব ভেবে রেখেছি। ঠিক পাশের বাড়িটাও বেশ দূর। মাঝখানে একটা খেতের আইল পার হতে হয়।
ঝিম ধরা একাকী দুপুরে বুঝি চোখ লেগে এসেছিল। শুয়ে ছিলাম বড় বেডরুমটায়, হঠাৎ মনে হলো ভাইয়া রুমে এসে ঢুকেছে। আমার দিকে ভাইয়া তাকাতেই বুকটা ধড়াস করে উঠল। ভাইয়ার চোখে কোন মণি নেই। অদ্ভুত সাদা। আমি চিৎকার দিয়ে উঠতেই ঘুমটা ভেঙে গেল। শীতকালেও আমি ঘেমে জবজবে হয়ে গিয়েছি। এত বাস্তব! এত বীভৎস স্বপ্ন! ঘুমটাও গেল, মনটাও দমে গেল। জায়গাটা আর ভাল লাগছিল না কিছুতেই। হাত-পা বিবশ হয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল পিছন থেকে কেউ এসে ঠাণ্ডা হাত রাখবে কাঁধে অথবা বিছানার নিচ থেকে হাত বাড়িয়ে আমার পা টেনে ধরবে কেউ! সে এক অসম্ভব আতঙ্ক। ভাইয়া না আসা পর্যন্ত আমি প্রায় মরে গিয়েছিলাম। ভাইয়া আসতেই ভয় কমে গেল। তাকে আর কিছু বললাম না।
আমি ওটাকে নিছক স্বপ্নই ভেবেছিলাম। তাই গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু আমি রোজ একই স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। কখনও ভাইয়া, কখনও মা, কখনও বাবা এসে মণিহীন চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে! সে এক তীব্র আতঙ্ক! কিন্তু কী যেন হত আমার। ভাইয়া আসলেই আমি আর স্বপ্নের কথা বলতে পারতাম না। কী যেন বাধা দিত। পরদিন ভাইয়া আবার অফিসে যাওয়ার পর থেকে আমি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়তাম। ঘুমাতে চাইতাম না। কিন্তু ঠিক ওই সময়েই জাদুবলে কে যেন সোনার কাঠি ছুঁইয়ে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে ভয়ের জগতে নিয়ে যেত। অসম্ভব এক ভয়, আর ভয় পাওয়ার ভয়ঙ্কর এক নেশা! বুয়া সবসময় থাকত, কিন্তু তাও আমি স্বপ্ন থেকে রেহাই পেতাম না।
একমাসের ভিতরেই নতুন বাসা ঠিক হলো, কিন্তু ততদিনে আমি শুকিয়ে কাঠি-কাঠি হয়ে গেলাম। রোজ ভয় পেতাম। আমি যেন সম্মোহিত ছিলাম। স্বপ্নের কথা বলতে গেলেই আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসত। কাউকে বলতে পারতাম না। তাই বাসা পরিবর্তনের কথায় আমার চেয়ে খুশি আর কেউ হয়নি।
চলে যাওয়ার আগের সন্ধ্যায় ভাইয়া আর আমি সব গুছিয়ে নিচ্ছিলাম। তখন ভাইয়ার এক কলিগ আর তার স্ত্রী এসে উপস্থিত হলেন। চা খেয়ে বিদায় নেয়ার সময় ওই ভাবী বললেন, তোমরা বেশ অনেকদিন থেকে গেলে এখানে। কিন্তু জানো, এই বাড়িতে কেউ থাকতে পারে না। পিশাচের দল নাকি আপনজন সেজে এসে ভয় দেখায়! তোমরা কীভাবে থাকলে বলো তো? বলতেই-বলতেই ভাবীর চোখ পুরো সাদা হয়ে গেল!
তারপর আর আমার কিছু মনে নেই। বোধহয় হার্টফেলই করেছিলাম। সে থেকেই আছি, বেশ আছি। শুধু জানি যে মরে গিয়েছি। একদিন আয়না দেখেছিলাম, দিব্যি ছায়া পড়ে।
আমার চোখও এখন একদম সাদা!
অন্য কিছু – রতন চক্রবর্তী
এক
লোকটা জবুথুবু হয়ে বাস থেকে নামল। ও আগে আর আমি পিছনে। নেমেই হুড়মুড় করে পড়ে গেল। আমি লোকটাকে ধরে উঠালাম। লোকটার চোখ দুটো বড় বড় হয়ে আছে, আতঙ্কে। আমার দুবাহুর মধ্যে কেঁপে কেঁপে উঠছে সে। বয়সে প্রায় আমার মতই ইয়াং। গায়ের রং চাপা ফুলের মত ফর্সা। অত্যন্ত সুপুরুষ। মেয়েরা এমন ধরনের পুরুষকে পছন্দ করে। গায়ে সস্তা দরের জামা আর লুঙ্গি, যা তার রূপের সাথে মানাচ্ছে না। রাস্তার পাশেই একটা চায়ের দোকান, সামনে। একটা লম্বা বেঞ্চ পাতা। তাতে লোকজন বসে। এখন অবশ্য কোনও খদ্দের নেই। ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে খদ্দের না থাকারই কথা। আমি লোকটাকে ওখানে বসালাম। জিজ্ঞেস করলাম, কিছু খেয়েছেন? চেহারা দেখেই মনে হচ্ছিল সে কিছু খায়নি। অন্তত দুদিন যে পেটে কিছু পড়েনি আমি নিশ্চিত।
– মাথা নেড়ে না করল সে। এই দুপুরে চা খাওয়ার চেয়ে ভাত খাওয়া ভাল। দোকানিকে জিজ্ঞেস করলাম এখানে। আশপাশে কোনও হোটেল আছে কিনা। দোকানি বলল, দশ মিনিট মত হাঁটলে একটা বাজার মত পাওয়া যাবে। ওখানে হোটেল আছে। ভাত রুটি সবই পাওয়া যাবে। অনেকের মনে হতে পারে, রাস্তায় কত লোকই তো কত রকম ঝামেলায় পড়ে। হঠাৎ করে এই লোকটার জন্য আমার দরদ উথলে উঠল কেন? আসলে ওর চেহারাটা এমনই বনেদি টাইপ যে মনে হচ্ছিল এমন পরিস্থিতিতে সে কখনও পড়েনি। তার প্রতি কেন যেন একটা টান অনুভব করছিলাম। আর তার আতঙ্কিত চোখের ভাষায় অজানা এক রহস্য খেলা করছিল, যা আমাকে ভীষণ টানছিল।
হোটেলে বসে গোগ্রাসে লোকটা ভাত খেল। পানি খেল। তারপর তাকে বেশ সুস্থ মনে হলো। এতক্ষণে কথা বলল সে, থ্যাঙ্কস।
লোকটা শিক্ষিত, বুঝতে পারলাম। শিক্ষিত লোকের কথার ধরন অন্য রকম। আমি ভণিতায় না গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, ঘটনা কী, বলেন।
লোকটা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, একটা সিগারেট খাওয়াবেন?
আমি বললাম, স্যরি, আমার আগেই জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। এক্ষুণি আনিয়ে দিচ্ছি।
হাঁটতে হাঁটতে আমরা হাইওয়ের পাশে একটা গাছতলায় এসে দাঁড়ালাম। তারপর লোকটা ওই গাছতলাতেই বসে পড়ল। আমিও বসলাম। রাস্তা ধরে সাঁই সাঁই বাস-ট্রাক বেরিয়ে যাচ্ছে আমাদের সামনে দিয়ে। সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে লোকটা তার গল্প শুরু করল। কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর গল্প তার কাছে শুনব সেটা আমি আশা করিনি। তার ভাষাতেই গল্পটা তুলে দিলাম:
আমি বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। দাদাজান নাম রেখেছেন আরমান। গ্রামে আমাদের বিশাল অবস্থা। আমার বাবাকে এক নামে সবাই চেনে। এলাকায় তাঁর প্রতিপত্তি আছে। অনেকেই তাকে ইলেকশান করতে বলেছে, কিন্তু তিনি ওসর পছন্দ করতেন না। আমাকে শহরে রেখে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। বি.কম. পাশ করার পর বাবা বললেন, তাঁর ব্যবসা যেন দেখাশুনা করি। গঞ্জের বাজারে আমাদের চালের আড়ৎ। আমি আর আপত্তি করলাম না। বাবার ব্যবসা দেখাশুনা করতে লাগলাম। দাদাজান বাড়িতেই থাকতেন। ফলফলাদির বাগান আছে। ফুলের বাগান আছে। তাই। দেখাশুনা করতেন। আমি ব্যবসাটা ধরে ফেলার পর বাবাও দাদাজানকে সঙ্গ দিতেন। এভাবেই দিন কাটছিল আমার। এদিকে মা এবার সুযোগ পেয়ে বসলেন। আমাকে বিয়ে করতে হবে। দক্ষিণ পাড়ার পারভীনের সঙ্গে আমার প্রেম ছিল। মাকে জানালাম সে কথা। কেউ কোনও আপত্তি তুলল না। উভয় পক্ষের কথা মত বিয়ের দিনও ঠিক হলো। কিন্তু সেই বিয়ে আর হলো না। তার আগেই আমার ভাগ্যে নেমে এল ভয়ানক বিপর্যয়।
মাছ ধরা ছিল আমার একমাত্র শখ। ভরা বর্ষায়, বৃষ্টিতে ভিজে, গভীর রাতে, যখনই সুযোগ পেতাম মাছ ধরতে যেতাম। মাছের ভাগ্যও ছিল আমার ভাল। কোনওদিনই খালি হাতে ফিরতাম না। বন্ধু-বান্ধবরা আমাকে তাই মাছকুমার বলেই ডাকে। আমার বাবারও শখ ছিল মাছ ধরার। আমি ছোটবেলা থেকেই দেখতাম বাবাও রাত নেই দিন নেই, বৃষ্টি বাদল নেই, সুযোগ পেলেই মাছ ধরতেন। সে যাই হোক, বাবার ওই রোগটা আমাকেও পেয়েছে। মা আমাকে মানা করতেন। বলতেন, রাত-বিরাতে যাস না, বাবা। ওদের মাছের প্রতি বেজায় লোভ। শেষে ঘাড়-টাড় না আবার মটকে দেয়। আমি শুনে হাসতাম। আমাদের বাড়ির পাশে একটা বিশাল বাঁশ ঝাড়। তার পাশেই একটা পুকুর। সবাই ওটাকে বলে তারা পুষ্করিণী। কোনও এক রাতে নাকি ওটাতে একটা বড় তারা খসে পড়েছিল আকাশ থেকে। তখন থেকে ওটার ওই নাম।
সেই তারা পুষ্করিণীর পাড়ে কচু ঘেঁচু আর বাঁশের জঙ্গলে নাকি মেন্দির মা বলে এক পেতনী থাকত। বাবা যখন রাতে বৃষ্টির পানিতে পুকুর পাড়ে উজিয়ে ওঠা (পুকুর থেকে লাফিয়ে পাড়ে ওঠা) কৈ মাছ ধরে বাড়ি ফিরতেন, তখন প্রায়ই দেখতেন বাঁশ বাগানের কাছে জবুথুবু হয়ে বসে আছে কেউ। বাবা জিজ্ঞেস করতেন, কে গো, মেন্দির মা নাকি? মেন্দির মা জবাব দিত, ওঁ। বাবা তার থলে থেকে দুটো কই মাছ ছুঁড়ে দিতেন মেন্দির মার দিকে। যেদিন বাবা মাছ দিতেন না সেদিন নাকি স্বরে আওয়াজ হত, কীরে, মাছ দিলি না? ওই সব আমরা ছোট থাকতে শুনতাম। তাই মার ওই ঘাড় ভাঙার কথা খুব একটা আমল দিতাম না। কিন্তু এখন সব কিছু হারিয়ে বুঝতে পারছি মায়ের কথা আমল দেয়া উচিত ছিল। মায়ের কথা শুনলে আজ আর আমাকে সব হারাতে হত না… থামল আরমান। একটা সিগারেট ধরাল। কিছুক্ষণ সিগারেট টানল। তারপর ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার শুরু করল।
দুই
বর্ষাকালের একদিন। সেদিন সারা দিন ধরে বৃষ্টি ঝরেছে। সন্ধ্যা হলো, রাত হলো। কিন্তু বৃষ্টির বিরাম নেই। তবে একটু কমে এসেছে। শুনেছি সোনা বিলে নানা রকম মাছ পানিতে নিত্য ঘাই মারছে। ঝাঁকে ঝাকে মাছ। বৃষ্টির পানিতে মাছেদের যেন আনন্দ। আমি আর নিজেকে ঘরে ধরে রাখতে পারলাম না। মা মানা করলেন। কিন্তু আমি শুনলাম না। ছাতা, ছিপ আর একটা চার ব্যাটারির টর্চও নিলাম। বড় একটা অ্যালিউমিনিয়ামের হাঁড়ির গলায় দড়ি বেঁধে : ওটাও নিয়ে নিলাম, মাছ রাখার জন্য। সোনা বিলের পাড়ে একটা ছাতিম গাছ আছে। ওটাই আমার বসার প্রিয় জায়গা। এর আশপাশটা ঝোঁপ-জঙ্গলে ভরা। নানা রকম গাছ। কিন্তু ছাতিম গাছের তলাটা আমি পরিষ্কার করে নিয়েছি।
চারদিক নীরব। ঝিঁঝিরাও ডাকছে না। কালো অন্ধকার। ছাতিম গাছটার তলায় পৌঁছে বিলের পানিতে টর্চের আলো ফেললাম। নিকষ কালো জলেও কয়েকটা মাছ হুটোপুটি করতে দেখে খুশি হলাম। বসে গেলাম ছাতিম গাছতলায়। বঁড়শিতে মাছের টোপ গেঁথে ছুঁড়ে দিলাম পানিতে।
টপাটপ মাছ ধরতে শুরু করে দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যে হাঁড়িটা প্রায় মাছে ভরে গেল। ঠিক তখনই আওয়াজটা শুনতে পেলাম। কেউ একজন ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কান পাতলাম। কান্নাটা আসছে আমার ডান পাশ থেকে। আমার ডান পাশে গজ পাঁচেক দূরে একটা আম গাছ। পাশে ঝোঁপ-জঙ্গল। আমি টর্চের আলো ফেললাম ওদিকে। সাথে সাথে চমকে গেলাম। একটা মেয়ে মানুষ ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর হাতের দড়িটা ছুঁড়ে দিচ্ছে কিছুটা নিচু হয়ে থাকা আম গাছের একটা ডালে। মুহূর্তে বুঝে গেলাম, গলায় দড়ি দিয়ে ফাঁস নিতে যাচ্ছে কোনও হতভাগী। আমি ছিপ ফেলে দৌড়ে গেলাম তার দিকে। টেনে তাকে নিয়ে এলাম ছাতিম গাছতলায়। তখনও সে কাঁদছে। জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে?
তার মুখ থেকে একটা কথাও বের করতে পারলাম না। ভাল বিপাকে পড়লাম। কে জানে কার সাথে ঝগড়া করে কিংবা কীসের দুঃখে মরতে এসেছে! এখন ফেলেও যেতে পারব না। তাকে নিয়ে বাড়ির পথ ধরলাম। ততক্ষণে বৃষ্টি ধরে এসেছে। বাড়িতে মা জেগে ছিলেন। দরজায় টোকা দিতেই খুলে দিলেন। আমি কীভাবে কী বলব ভেবে পেলাম না।
তারপরও সাহসে ভর করে সব কিছু খুলে বললাম। মা কতক্ষণ থ মেরে রইলেন। তারপর কুপিটা ওই মেয়ের মুখের কাছে ধরলেন। সাথে সাথে অস্ফুট একটা শব্দ করে হাত থেকে জ্বলন্ত কুপিটা ফেলে দিলেন। চমকে গেছেন ভীষণভাবে। চমকে গেছি আমিও! এমন রূপও মানুষের হয়! মা আর কিছু বললেন না। রাতটা অস্থিরতার মধ্যে কেটে গেল। মা তাকে শোবার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিন্তু আমি লক্ষ করলাম মার মধ্যে একটা আতঙ্ক বিরাজ করছে। পরদিন সকালে মা আমাকে ফিসফিস করে বললেন, পুকুর ঘাটে আয়। আমি ঘাটে গেলে মা আমাকে বললেন, বাবা, এ কাকে নিয়ে এলি তুই! এ তো বাবা মানুষ নয়! মানুষের এত রূপ হয় না। এ অন্য কিছু। খোদা জানে কী গজব নাজিল হবে এবার আমার সংসারে! আমি মাকে বললাম, মা, এ তোমার মনের ভুল। এসব ভেব না তো। আর কথা না বাড়িয়ে চলে এলাম
কিন্তু মা আমার ভুল যে বলেননি তার প্রমাণ পেলাম পরদিন। তার আগে বলে নিই, মার সাথে পুকুর ঘাটে কথা বলে আমি গদিতে চলে আসি। বিকেলে বাড়ি ফিরে শুনি সারাদিন ওই মেয়ে অন্ধকার কোনায় বসে থেকেছে। মা এত করে ডাকার পরও বের হয়ে আসেনি। কিছু খায়নি ও। কিন্তু সন্ধে হতে না হতেই তার মধ্যে উতলা ভাব লক্ষ করলাম। কোণ থেকে বেরিয়ে এল সে। স্বাভাবিক নিয়মে চলাফেরা করল। আমার দিকে কটাক্ষে চেয়ে একটু যেন মুচকি হাসতেও দেখলাম। আমার চোখের ভুলও হতে পারে। কিন্তু কথা বলল না, কিছু একটু খেলও না। সেদিন রাতে ভাল ঘুম হলো আমার। কিন্তু সকালবেলা বাড়ির কাজের লোক মতি মিয়ার চিৎকার-চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল। ঘরের বাইরে বেরিয়েই থমকে গেলাম। চোখ বড় বড় হয়ে গেল।
আমার প্রিয় কুকুরটাকে কে বা কীসে যেন বীভৎসভাবে পেট চিরে নাড়ি ভুড়ি বের করে হত্যা করেছে। চিৎ হয়ে শুয়ে আছে ওটা, আতঙ্কিত চোখে চেয়ে। কী এমন জন্তুর আবির্ভাব হলো এলাকায় কে জানে? ভাবতে থাকলাম আমি। কোনও কিনারা করতে পারলাম না। কিন্তু ওই আশ্রিতা মেয়ে ঘরের কোণেই রয়ে গেল। দিনের বেলাতেই সে এমন করে। মতি মিয়াকে অন্য রকম মনে হলো। সে চোখ বড় বড় করে পাগলের মত আচরণ করতে থাকল। আর বলতে থাকল, আমি দেখেছি, সব দেখেছি, কিন্তু বলব না, আমি বলব না। মতিকে ডাকলাম, মতি, ঘরে আয়, কী দেখেছিস, আমাকে বল।
সে আরও ভয় পেয়ে গেল। চিৎকার করে বলল, না, ওঘরে আমি যাব না। আমি দেখেছি, সব দেখেছি। চিৎকার করতে করতে সে বেরিয়ে গেল। রাতে সে জেগে থাকে। হয়তো কিছু দেখেছে। কিংবা কুকুরটাকে খুন করতে দেখেছে। খুনিকে।
মা আমাকে ফিসফিস করে বলল, সব ওই ডাইনীটার কাজ। ওটা যেদিন থেকে বাড়িতে এসেছে সেদিন থেকেই শুরু।
আমার জন্য আরও বিপর্যয় অপেক্ষা করছিল। মা বুঝতে পারলেও আমি বুঝিনি। কিন্তু পরদিন সকালে যখন মতি মিয়ার লাশ পাওয়া গেল তারা পুষ্করিণীর পাড়ে তখন আমি সত্যিকারের ভয় পেলাম। তারও পেটটা ছিল চিরা। দেহের বিভিন্ন জায়গা থেকে কেউ খাবলে খুবলে মাংস খেয়ে গেছে। পুলিশ-ফুলিশ, নানা ঝক্কি ঝামেলা শেষ করতে করতেই দিন শেষ হলো। গ্রামের লোকজন আমাদের বাড়িটাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করল। ওরা বলে আমাদের বাড়ির চারপাশে নাকি। কিছু একটা ঘুরে বেড়ায় রাতে। কিন্তু আমাদের বাড়িতে আশ্রয় নেয়া মেয়েটির এদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। সে এখন অনেকটা স্বাভাবিক। কথাটথাও বলে। কিন্তু নিজের পরিচয় বলে না। তবে এখন আর আমাদের বাড়ির আশপাশে কোনও অঘটন ঘটে না। গোরস্থানের কবর খুঁড়ে দুএকটা লাশ কে বা কিছুতে খাবলে খেয়ে গেছে এমন খবর আসে। ওটা শেয়ালের কাজ হতে পারে, ভেবে আমরা গা করি না। এর মধ্যে আমার বিয়ে ঠিক হয়। যাকে আমি ভালবাসি তার সাথেই বিয়ে। পারভীনের সাথে।
কিন্তু বিয়ে আমার আর পারভীনকে করা হলো না। যেদিন বিয়ে সেদিন সকালে তার লাশ পাওয়া গেল বাশ ঝাড়ের মধ্যে। কেউ যেন তার দেহটা খুবলে খেয়ে গেছে! এদিকে বিয়ের কার্ড বিতরণ হয়ে গেছে। দাওয়াত দেওয়া হয়ে গেছে। আত্মীয়-স্বজনে বাড়ি গম গম। বাবা আর দাদাজানের ইচ্ছায় আমার বিয়ে হলো ওই মেয়ের সাথে। যাকে আমি বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছি। মার ইচ্ছে ছিল না। মা তাকে তখনও ডাইনীই ভাবত।
বাসর রাত আমার হলো না। বিছানায় যেতেই আমার বউ আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল।
সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মায়ের সাথে দেখা হতেই বুঝলাম কিছু একটা হয়েছে। আমি মাকে জিজ্ঞেস করলাম,! কী হয়েছে, মা?
মা আমাকে বললেন, পুকুর পাড়ে আয়।
আমি গেলাম। মা বললেন, কাল রাতে বৌমাকে মাঝরাতে ঘর থেকে বের হতে দেখলাম! আমিও চুপি চুপি তার পিছু নিলাম, কিছুদূর যেতেই দেখি সে গোরস্থানের দিকে হাঁটা দিয়েছে… হঠাৎ থেমে গেলেন মা। আতঙ্কিত চোখে তাকিয়ে থাকলেন একদিকে। তার তাকানো লক্ষ্য করে ও দেখলাম তিনি জানালার দিকে তাকিয়ে আছেন। আর আমার ঘরের জানালা থেকে আমার বউ তীব্র চোখে তাকিয়ে আছে এই দিকে! আমাকে দেখেই সরে গেল সে! আমার মা-ও আমার সামনে থেকে দ্রুত সরে গেলেন।
সেদিন রাতেই খুন হলেন মা! চরম আক্রোশে কেউ তার দেহটা ছিন্নভিন্ন করেছে। পুকুর পাড়েই পড়ে ছিল তার লাশ। এবার যেন আমি একটু একটু বুঝতে পারলাম। আসলেই আমি এক পিশাচ নারীকে বিয়ে করেছি। কিন্তু আমি যে তাকে চিনে ফেলেছি, তা তাকে বুঝতে দিলাম না। আমার মা যে মারা গেল তার মধ্যে কোনও অনুশোচনা দেখতে পেলাম না। এখন বুঝতে পারলাম পারভীনকে কে মেরেছে। আমার স্ত্রী হবার জন্যই সে একাজ করেছে।
সেদিন রাতে সে আমার সাথে ভাল ব্যবহার করল। আমরা মিলিত হলাম। আমার ইচ্ছে ছিল না। মা হারানোর বেদনা মনে তখনও ছিল। যা যাবে না কখনও। মনে মনে দৃঢ় সঙ্কল্প করলাম, আজ রাতে আর ঘুমাব না। ঘুমের ভান করে পড়ে থাকব। তারপর ডাইনীটা ঘর থেকে বের হলে পিছু নেব। কে বলবে এমন সুন্দর মুখের একটা মানুষ পিশাচ। আমার বিশ্বাস হতে চাইছিল না। আমাকে নিজের চোখে দেখতে হবে।
সে যখন নিশ্চিত হলো আমি ঘুমিয়ে পড়েছি, বিছানা থেকে নামল। থমকে দাঁড়াল ঘরের মেঝেতে। নিশ্চিত হতে চাইছে ভালভাবে। তারপর দরজা খোলার আওয়াজ পেলাম। বাইরে থেকে দরজাটা ভেজিয়ে নেমে গেল সে উঠানে। আমি আরও কতক্ষণ মটকা মেরে পড়ে রইলাম। তারপর আস্তে করে নেমে এলাম নিচে। বাইরে বেরিয়ে এলাম। নিঝুম রাত। হালকা বাতাস বইছে। তার গন্তব্য আমি জানি। আজ একজনকে কবর দেয়া হয়েছে। আমি জানি তার গন্তব্য গোরস্থান। বাড়ির সীমানা ছাড়াতেই আমার সামনে দুজনকে দেখতে পেলাম। চমকে উঠলাম আমি। দাদাজান আর বাবা। ওঁরাও তা হলে পিশাচটার পিছু নিয়েছেন। মা মারা যাবার পর বাবা ভেঙে পড়েছিলেন। কিন্তু তার মনেও যে ডাইনীটাকে হাতে-নাতে ধরার ইচ্ছা ছিল তা জানতাম না। তারা বাপ ছেলে সাবধানে এগিয়ে চললেন। আরও কিছুদূর গেলেই একটা বড় তেঁতুল গাছ পড়বে রাস্তার পাশে। একটা মোটা ডাল রাস্তার উপর ঝুঁকে আছে, মাটি থেকে দশ বারো হাত উপরে।
আকাশ ছিল পরিষ্কার। রাস্তায় ঝুঁকে থাকা তেঁতুল গাছের ডালটার উপরের আকাশটা ভালভাবেই দেখা যাচ্ছিল। পরিষ্কার আকাশে ক্ষয়ে যাওয়া চাঁদ। সে আলোতেও ওটাকে দেখতে পেলাম! সামনে থেকে বাবা আর দাদাজান থমকে দাঁড়ালেন। আমি তাদের কাছ থেকে হাত পাঁচেক দূরে একটা কাঁঠাল গাছের আড়াল নিলাম। ওটা বসে ছিল তেঁতুল গাছের ডালটায়। বিশাল দেহ। মাথার চুলগুলো মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। তীব্র চোখে তাকিয়ে ছিল রাস্তার দিকে। তার চোখ দুটো হিংস্র শ্বাপদের মত জ্বলজ্বল করছিল। বাবা আর দাদাজান তার কাছে ধরা পড়ে গেছেন! খিলখিল করে হেসে। উঠল পিশাচ নারী। তার হাসিতে খান খান হয়ে ভেঙে পড়ল রাতের নীরবতা। তারপর যা ঘটল তা এতদিন রূপকথাতেই শুনেছিলাম! হঠাৎ একটা হাত তীব্র গতিতে ছুটে এল বাবা আর দাদাজানের দিকে। এক থাপ্পড়ে দুজন ঢলে পড়লেন মাটিতে। বুঝতে পারলাম ওঁরা আর এই জগতে নেই। আতঙ্কে বোবা হয়ে গেলাম। আমার পা যেন পেরেক দিয়ে কেউ গেঁথে দিয়েছে। ওটা গাছ থেকে নেমে এল। আবার স্বাভাবিক রূপ দেখা গেল তার। বাবা আর দাদাজানের লাশের সামনে এসে বসে গেল। আমি জানি এখন ওটা খেতে শুরু করবে ওঁদের লাশ। আমার চোখ ফেটে জল এল। তারপর ভীত পায়ে ফিরে এলাম ঘরে। দরজা ভেজিয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। মুক্তির উপায় ভাবতে লাগলাম। একদিনের ব্যবধানে মা-বাবা আর দাদাজানকে হারিয়েও ঘুম এসে গেল আমার চোখে। কখন। আমার পিশাচী বউ ফিরে এসেছে জানতে পারিনি।
পরদিন আমার বাবা আর দাদাজানের লাশ কোথাও পেলাম না। এমনকী তাদের হাড়গুলোও নয়। রাক্ষুসী ওঁদের সবটাই খেয়ে ফেলেছে নাকি? দিনে দিনে ওর ক্ষুধা বেড়েই চলেছে! আমাকে পালাতে হবে। আমার মনের কথা যেন সে বুঝে ফেলল। আমার কানের কাছে মুখ এনে হিসহিসিয়ে বলল, ওই চেষ্টাও কোরো না। তুমি পালিয়ে কোথাও যেতে পারবে না। আমি জানি তুমি কাল রাতের ঘটনা সব দেখেছ। কাউকে ওকথা বলতেও যেয়ো না। তোমাকে আমি মারব না। তোমার আশ্রয় আমার দরকার। তোমার স্ত্রী হিসেবে থেকেই আমি আমার চাহিদা মিটিয়ে যাব। আর আমার পিছু নিতে চেষ্টা করবে না, আরমান। আবারও বলছি কাউকে বলবে না। বলেছ তো মরেছ। যাও, স্বাভাবিক মানুষের মত বাজারে যাও। ব্যবসাপাতি দেখ। দুপুরে বাড়িতে আসবে আর আমি লক্ষ্মী বউয়ের মত ভাত বেড়ে তোমার জন্য অপেক্ষা করব। বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল ডাইনীটা।
আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। আমার জানামতে। একজন ভাল তান্ত্রিক ছিল। তার নাম ছিল গোখরোনাথ। ভূত প্রেতের উপদ্রব থেকে রক্ষা করতে ওস্তাদ। তার সাথে দেখা করলাম। সব কিছু বললাম। শুনে বলল, ভয় পাসনে, বেটা। ওটার ব্যবস্থা আমি করব। আজ সন্ধেবেলা যাব তোর বাড়িতে।
আমি বাড়ি ফিরে এলাম। আমাকে যত্ন করে ভাত বেড়ে দিল আমার বউ। আমি খেলাম না কিছু। সেও কিছু বলল না। মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। এদিকে সন্ধে হয়ে এল। আমি। অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিন্তু গোখরোনাথ আসছে না। আমার বউ বলল, কারও জন্য অপেক্ষা করছ মনে হচ্ছে?
আমি কিছু বললাম না। সন্ধে গিয়ে যখন রাত হব হব করছে তখন আমি ভাবলাম, না, দেখে আসা দরকার। হয়তো তান্ত্রিক আমার বাড়ির পথ ভুল করেছে। না-ও চিনতে পারে। আমি উঠন ছেড়ে বের হব তখন আমার পিশাচী বউ হেসে উঠল। বলল, গোখরোনাথকে এগিয়ে আনতে যাচ্ছ? ঠিক আছে যাও। আমি অপেক্ষা করছি। বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল।
তখনই আমার বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। বুঝতে পারলাম গোখরোনাথ আর নেই। এও সম্ভব!
তবু আমি পথে নামলাম। কিছুদূর এগুতেই অনেক। লোকের ভিড় দেখে এগিয়ে গেলাম। কাছে গিয়ে দেখলাম টর্চ জেলে দাঁড়িয়ে আছে অনেক লোক। তাদের আলো রাস্তার ওপর পড়ে থাকা লোকটার দিকে। তার দিকে তাকিয়ে আতঙ্কের একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে। ওই ডাইনী কেমন করে আমার বাড়ির মধ্যে থেকেও গোখরোনাথকে মেরে ফেলল? গোখরোনাথের মুখ থেকে রক্ত বের হয়ে রাস্তার মাটি কালচে হয়ে আছে। চোখ দুটোতে সীমাহীন আতঙ্ক। আমি আর কিছু ভাবতে পারলাম না। বিষণ্ণ মনে ফিরে এলাম বাড়ি। আমি জানি রাতের বেলা ওর ক্ষমতা বেড়ে যায়। তাই রাতে পালাতে চাইলেও পারব না। পালাতে হবে দিনের বেলা। বাড়ি ফিরতেই যেন কিছু হয়নি এমনভাবে আমাকে ঘরে ডাকল সে। আমার পাশে বসল। বলল, কেন। এসব করতে যাও? তুমি আমার ক্ষমতা হয়তো জানতে না। এখন জানলে তো। আর ভুলেও এমন চেষ্টা কোরো না।
আমি কিছু বললাম না। রাতে আমার ঘুম এল না। মাঝরাতে সে বেরিয়ে গেল। শেষ রাতের দিকে ফিরে এল। আর আমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকল। মুখ থেকে পচা নর মাংসের গন্ধ এল। আমার গা ঘিন ঘিন করতে লাগল, বমি আসার অবস্থা হলো। কিন্তু আমি নিশ্চুপ শুয়ে রইলাম। পরদিন সকালে যেন কিছুই হয়নি, এমনভাবে বেরিয়ে এলাম। যেন আমার গদিতে আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যাচ্ছি। তারপর পালালাম। হাইওয়ে ধরে হাঁটতে হাঁটতে কাছের বাস স্টপেজে এসে বাসে উঠে বসলাম। কোথায় যাচ্ছি, সেটা বড় কথা নয়। জানতেও চাইনি। আমার একটাই উদ্দেশ্য, ওটার কাছ থেকে দূরে চলে যাওয়া। তারপর আপনার সাথে দেখা… থামল আরমান। অনেকক্ষণ কথা বলার জন্য হাঁফাচ্ছে।
আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে দিলাম ওকে। সিগারেটে একটা টান দিয়েই ছুঁড়ে ফেলে দিল ওটা। চমকে উঠে দাঁড়াল। বলল, ওহ, মাই গড! ও বলেছিল এই কথা যেন কাউকে না বলি। ওর আসল রূপ যেন কাউকে ফাস না করি। তা হলে আমাকেও সে খুন করবে!
আমি তার সাথে সাথে উঠে দাঁড়ালাম। ততক্ষণে চারদিকে
সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে হাইওয়েতে। হঠাৎ একটা গরম। হাওয়া ঝাঁপটা মারল। একটা চিৎকার শুনলাম। আরমানের চিৎকার। ঝটকা দিয়ে ওর শরীরটা দশ ফুট উপরে উঠে গেল। ঝড়ো গতিতে তার দেহটা শূন্যে ভেসে ধেয়ে গেল হাইওয়ের মাঝখানে। ধপ্ করে আছড়ে পড়ল পিচের রাস্তায়। ততোধিক ঝড়ো গতিতে ধেয়ে আসছিল একটা ট্রাক! একটা মাত্র আর্তচিৎকারই দিতে পেরেছিল আরমান। ট্রাকটা ওকে পিষে চলে গেল দ্রুত গতিতে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ঘটে গেল ঘটনাটা। কয়েকজন পথচারী দৌড়ে এল ঘটনাস্থলে। আমিও গেলাম। কেউ একজন পুলিশ স্টেশনে মোবাইল করল।
পিশাচী তার কথা রেখেছে। ততক্ষণে রাত হতে চলেছে। পুলিশের সাইরেন শোনা গেল। বেচারা আরমান পালিয়েও বাঁচতে পারল না।
আমি বাড়ি ফিরছিলাম। আরমানের গল্পটা তখনও মাথায় আলোড়ন তুলছিল। মহল্লার রাস্তায় পড়তেই গাটা ছম ছম করে উঠল। বাড়ি যেতে হলে একটা মাঠ পেরুতে হয়। ওটার কাছে আসতেই দেখতে পেলাম মাঠের পাশের চালতা গাছটার তলায় একটা মেয়ে, একটা দড়ি ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারছে গাছটার অপেক্ষাকৃত নিচু ডালটা লক্ষ্য করে। নিশ্চয়ই আত্মহত্যা করবে। রাস্তার ল্যাম্পপোস্টের আবছা আলোয় স্পষ্ট দেখলাম। ছুটে যেতে চাইলাম মেয়েটাকে বাঁচাতে। সহসা মনে পড়ল আরমানের কাহিনী। থমকে দাঁড়ালাম। ভয়ের একটা শীতল স্রোত অনুভব করলাম রক্তে। দ্রুত পা বাড়ালাম বাড়ির দিকে। আমি চাই না আমার অবস্থাও আরমানের মত হোক!
নিশি মিয়া – রাজীব চৌধুরী
নিশি মিয়াকে আমি সেদিনের আগে কখনও দেখিনি। দেখেছি তাও অনেক দিন হলো। হয়তো সময়ের হিসাবে বেশ কয়েক বছর গড়িয়ে গেছে। ঠিক মনে নেই কতদিন আগে। তবে তখন আমি মনে হয় ক্লাস ফাইভে কিংবা সিক্সে পড়ি। অনেক ছোট ছিলাম। গরমের ছুটিতে গিয়েছিলাম আমার গ্রামের বাড়িতে। সেখানে কেউ থাকে না। আমরা শহরেই থাকি। সেই জন্য মাঝে মাঝে আমার স্কুল ছুটি হলেই বাবা-মা আমাকে নিয়ে ছুটে যান আমাদের বাড়িতে।
আমাদের বাড়িটা বিশাল। বিশাল বলতে আক্ষরিক অর্থেই বিশাল। কিন্তু মানুষজন নেই বললেই চলে। আমার দাদার একমাত্র ছেলে আমার বাবা আর আমি আমার বাবার একমাত্র ছেলে। বাবা ব্যবসা দেখার জন্য শহরে চলে। এসেছেন। সাথে আমার লেখাপড়ার চিন্তাও মাথায় ছিল। সেই জন্য আমাকে শহরে নিয়ে এসে ভর্তি করিয়েছেন ভাল স্কুলে। কিন্তু বাবা গ্রামে কেয়ারটেকার রেখে সেখানকার সবকিছু পরিচালনা করেন। মাসে মাসে গ্রাম থেকে আমাদের জন্য চাল-ডাল আসে। আর প্রতি মৌসুমে আসে ফলফলাদি।
তবে কেয়ারটেকার বেচারা অনেক বুড়ো ছিল। আর সেই সুবাদে আমাদের বড় পুকুরের পাড়ে জংলায় আস্তানা গেড়েছিল নিশি মিয়া। খানিকটা পাগল টাইপের ছিল বলে তাকে আর কেউ ঘটায়নি। এমনকী আমার বাবাও নিশি মিয়াকে বেশ ভাল মতই দেখা-শোনা করার কথা বলে দিয়েছিলেন কেয়ারটেকারকে। কেন বলেছিলেন সেটা আমি জানি না।
সেদিন আমি বাড়িতে পৌঁছেই পাড়ার ছেলেদের সাথে মিলে খেলাধুলো করলাম। কিন্তু পরেরদিন বাবা যেই ছিপ নিয়ে পুকুর পাড়ে গেলেন, আমিও পিছু পিছু আরেকটা ছিপ নিয়ে বাবার থেকে দূরে আরেকটা ঘাটে বসে পড়লাম। বাবা শহুরে জীবনে ছিপ দিয়ে মাছ ধরতে পারেন না। তাই গ্রামে আসলেই বসে পড়েন বড় পুকুরের ধারে। আমিও বাবার কাছেই মাছ ধরা শিখেছি। কিন্তু আমার ছিপে মাছ সহজে আসে না। কী এক নেশা! এই নেশা সেই ক্লাস থ্রি থেকে আমাকে পেয়ে বসেছিল। মাঝে মাঝেই আমাকে নিয়ে বিভিন্ন লেকে মাছ ধরতে যেতেন বাবার। কিন্তু গ্রামে আসলেই আমাকে না বলেই চলে যান মাছ ধরতে। আর আমিও বাবার সাথে পাল্লা দিয়ে মাছ ধরার চেষ্টা করি।
সেদিনও আমি বসেছি মাছের আশায়। ছিপে কেঁচো লাগিয়ে বসে আছি তো বসে আছি-কিন্তু মাছ আসে না। ইচ্ছে ছিল বাবার আগেই আমার মাছ আসবে ছিপে। কিন্তু আসে না। আমিও বসে আছি।
বাবা, এভাবে বসলি তো একটাও মাছ পাইবা না, পেছন থেকে ভাঙা ভাঙা গলায় কে যেন বলে উঠল।
পেছনে তাকিয়েই আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেলাম। ছোট্ট হৃৎপিণ্ড আমার লাফাতে শুরু করল পাগলের মত। আমি বাবা বলে চিৎকার করতেও ভুলে গেলাম প্রায়। লোকটা লাল রঙের একটা নেংটী পরা। সারা শরীরে আর কিছুই নেই। জায়গায় জায়গায় বড় বড় কিছু তাবিজ ঝোলানো।
জটপাকানো চুল দাড়ির ভিতর দুটো লালচে চোখ। এই দেখে আমার ভয়ে কাঁপাকাপি অবস্থা।
লোকটা বলল, বাবা, ভয় পাইসো? ভয় পাইয়ো না, আমি তোমারে কিছু করুম না, বলেই বিকট চিৎকার করে একটা হাসি দিল সে ভাঙা গলায়।
আমার ততক্ষণে কিছুটা সাহস ফিরে এসেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী নাম আপনার?
আমার পাশে এসে ঘাটে বসতে বসতে বলল, আমারে
সবাই নিশি মিয়া নামে ডাকে।
এটা কেমন নাম?
হা হা হা-এটার কোনও মানে নাই, বলেই আমার দিকে হেসে হেসে তাকাল। আমার ততক্ষণে মজা লাগতে শুরু করেছে। কারণ সে আমার পাশে বসার সাথে সাথে আমি একটা মাছের টোপ গেলা টের পেয়েছি আমার হাতে। ছিপে টান মেরে মাছটাকে ধরে কোনওরকমে আমার পাশে রাখা বেতের ঝুড়িতে রাখলাম। ঝুড়িতে আমার সদ্য ধরা মাছটা লাফালাফি করছে। বঁড়শিতে আপন মনে আবার কেঁচো মেশানো বিস্কিটের দলা লাগিয়ে ছুঁড়ে দিলাম পানিতে
আর সাথে সাথে আরও একটা মাছ পেলাম। আমার পাশে মাছটাকে রাখতে রাখতে আমি খেয়াল করলাম, লোকটার শরীর থেকে কেমন যেন কাঁচা মাছের গন্ধ বের হচ্ছে। আমি পাত্তা দিলাম না। খানিকটা সরে এসে বসলাম। আর সাথে সাথে আরেকটা মাছ পেলাম আমি।
আপনি কী করেন? মাছটাকে ছিপ থেকে খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করলাম।
আমি? কিছু করি না, আবার অনেক কিছুই করি, বলেই খিক খিক করে হেসে ফেলল সে।
মানে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।
মানে আমি নিশি ডাকি মাঝে মইধ্যে।
এটা কী জিনিস? এটা হইল এমন জিনিস…যদি আমি সফল হই তাইলেও মানুষ মরে, সফল না হইলেও মানুষ মরে।
তা মানুষ মরার কথা শুনে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তড়িঘড়ি করে উঠে যাব, এমন সময় পেছন থেকে নিশি মিয়া আমাকে ডেকে বলল, বাবা, আমারে একটা মাছ দিয়া যাও, মুখের হাসি হাসি ভাবটা উধাও। সেখানে হুকুমের সুর।
আমিও ভয়ে একটা মাছ তাকে দিয়েই সেদিনের মত বিদায় নিলাম। বাসায় বাবার আগেই মাছ ধরে আনতে পারার খুশিতে সেদিন ভুলেই গেলাম নিশি মিয়ার কথা। কিন্তু আমার এখন মাঝে মাঝে মনে হয় সেদিন আমি মাছটা দেয়ার সাথে সাথে পেছন ঘুরে কাঁচা মাছটাই খাওয়া শুরু করেছিল নিশি মিয়া। হয়তো আমি ভুল দেখেছিলাম। হয়তো না। কে জানে।
পরের দুই দিন আমি নিশি মিয়াকে বেমালুম ভুলে গেলাম। কারণ টগর আর ওর মা-বাবা, মানে আমার ফুফা ফুফু এসেছিলেন আমাদের বাড়িতে বেড়াতে। আমার থেকে এক বছরের বড় টগর আমার সাথেই স্কুলে পড়ত। আর ওকে পেয়েই আমি ভুলে গেলাম সবকিছু। দুইজনে যত পারলাম দুষ্টামি করলাম। নিজেদের আমবাগান ফেলে আরেকজনের বাগানে হানা দিলাম। ইচ্ছেমত চুরি করা, ইচ্ছেমত ডাব খাওয়া-এভাবেই কেটে গেল তিনটা দিন।
পঞ্চম দিনে হঠাৎ করে সব আনন্দ থেমে গেল। সকাল বেলা ফুফা নাস্তা করে বাজারে গেছিলেন। সেখান থেকে লোকজন ধরাধরি করে আনল বাড়িতে। প্রচণ্ড বুকের ব্যথায় উনি কাতরাচ্ছেন। আমরা দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। ডাক্তার ডাকা হলো। উনি নিয়ে যেতে বললেন সদর হাসপাতালে। বাবা খুব দ্রুত ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। সেখানে ডাক্তার ওঁকে ওষুধ দিলেন। কিন্তু বুকের ব্যথা কমে না। আমরা সবাই হাসপাতালে ছিলাম। বাবা আমাকে আর টগরকে নিয়ে বাড়িতে চলে এলেন।
বাড়িতে এসেই কেয়ারটেকারকে দিয়ে ডাকালেন নিশি মিয়াকে। নিশি মিয়া আসার আগেই আমাকে আর টগরকে অন্য ঘরে পাঠিয়ে দিলেন বাবা। কিন্তু আমার কেন যেন সন্দেহ হলো। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে পর্দার আড়ালে থেকে ওঁদের কথা শুনলাম।
বাবা, আমার বোন-জামাইরে তুমি বাঁচাও, নিশি মিয়া।
নিশি মিয়া, বাঁচাইতে পারুম, তয় আমারে কাইল রাইত পর্যন্ত টাইম দেয়া লাগব।
বাবা, তোমাকে বিনিময়ে কী দেব?
নিশি মিয়া, বেশি কিছু না, শুধু আমারে দুইখান কাঁচা মাছ আর মুরগি দেবেন। পেটে বড় খিদা।
বাবা, আর যদি তুমি বাঁচাইতে না পারো?
নিশি মিয়া, না পারলে আমি আমার নিজের শইলের মাংস কাইটা খামু।
ওইটুকু শুনেই আমি দৌড়ে চলে গেলাম আমার ঘরে। সেখানে ঢুকেই কিছুক্ষণ ভয়ে কথা বলতে পারিনি। পরে টগরকে বলেছিলাম। কিন্তু সে কোনওভাবেই বিশ্বাস করেনি।
পরের দিন আমি দুইবার হাসপাতালে গিয়ে ফুফাঁকে দেখে এসেছি। ওঁর অবস্থা আরও খারাপের দিকে গেছে। কিছুক্ষণ উনি ঘুমান। আবার কিছুক্ষণ চিৎকার চেঁচামেচি করেন। এর মাঝে সন্ধ্যার দিকে নিশি মিয়া এসে দেখে গেছে। ওঁকে। আমি মায়ের কাছে শুনেছি নিশি মিয়া নাকি ফুফাঁকে কী একটা পানি খাইয়ে দিয়েই চলে গেছে কাজে। সেদিন সন্ধ্যায় টগর ছিল ওর বাবার সাথে। আমি একা একা কাটিয়েছি বাসায়। পাশের পাড়ার সুমন আর সুমি এসেছিল আমাদের বাড়িতে। সুমন এসেই আমাকে এক আজগুবি গল্প শোনাল। নিশি মিয়া নাকি ধুপ ধুনো নিয়ে তৈরি হয়ে গেছে। সে আজকে নিশি ডাকবে। প্রতি বাড়ি বাড়ি গিয়ে একবার ধুনো দেবে আর বাড়ির মানুষের নাম ধরে একবার একবার করে ডাকবে। যদি কেউ সেই ডাকে সাড়া দেয় তবে তার মরণ হবে। আর আমার ফুফা বেঁচে উঠবেন।
শুনে আমি ভয় পেয়ে গেলাম। সেদিন রাতে ঘুমাতে পারিনি। বাসায় বাবা ছিলেন নিচে। আমি আর মা ছিলাম উপরে। নিশি মিয়ার কাছে বলা ছিল সে যেন আমাদের বাড়ির ত্রিসীমানায়ও না আসে। আমাদের এই কারণে কোনও ভয় ছিল না। সারারাত ধরে আমি দুরুদুরু বুকে কেঁপেছি নিশি মিয়ার ডাক শোনার জন্য। হঠাৎ করে মনেও হয়েছিল কে যেন অনেক দূরে ডেকে ডেকে চলেছে। কিন্তু মনের ভুল মনে করে আমি আবার ঘুমিয়ে গেছি।
এর পরের দিনটা আমাদের জন্য অনেক খারাপ একটা দিন ছিল। ফুফু রাতের বেলাতেই মারা গেছেন। নিশি মিয়ার নিশি ডাক কোনও কাজ করতে পারেনি। লাশ নিয়ে যাওয়া হলো ফুফার বাড়িতে। সেখানে আমরা সবাই গেলাম। সবার মন খারাপ। ফুফু আর টগরের চোখের কান্না দেখে আমিও থাকতে পারিনি। অনেক কেঁদেছি। জলজ্যান্ত মানুষটাকে মরে যেতে দেখলাম আমি। মরে যাওয়া মানুষের শরীরের গন্ধ শুকলাম সেই প্রথম। ফুফাঁকে গোসল করানোর সময় ফুফার শরীরের দিকে তাকিয়ে কেন যেন মনে হচ্ছিল উনি মরেননি। ঘুমিয়ে আছেন মাত্র।
ফুফার দাফন সম্পন্ন করে সেদিন রাতে আমরা থেকে গেলাম ফুফুদের ঘরে। ওঁরা খুব একটা অবস্থাসম্পন্ন ছিলেন না। একটা কুঁড়ে ঘর ছিল ওদের। ফুফাঁকে যেখানে কবর দেয়া হয়েছে এর থেকে সামান্য দূরে একটা ডোবা আছে। সেখানে ওঁদের ঝুলন্ত পায়খানা ছিল। আর সামনে একটুকু উঠান-এই নিয়ে ছিল ওঁদের বাড়ি।
রাতে আমরা কোনও রকমে কিছু একটা খেয়ে শুয়ে পড়লাম। এক ঘরে আমি, টগর আর আম্মা। অন্য ঘরে ফুফু আর ওঁদের বাড়ির আরেকজন। আব্বা বাইরের ঘরে শুলেন। আর ঘরের ভেতর এই সময় প্রস্রাব আসলে একটা পিতলের পাত্রে করতে হবে এই ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু হঠাৎ আমার প্রচণ্ড পায়খানা ধরল। রাতের বেলা আমি আম্মাকে ডেকে তুলতে ভয় পেলাম। সারাদিন অনেক কেঁদে কেঁদে আম্মা মাত্র ঘুমিয়েছেন। আমি টগরকে ডেকে তুললাম। বললাম আমার সাথে যেন একটু বাইরে পায়খানার কাছে যায়। টগর ল্যাম্প জ্বেলে আমার সাথে আসল।
পায়খানা ছিল বাঁশের তৈরি। নিচের দিকে একটা সিমেন্টের পাত বসানো। তাতে একটা ফুটো। উপর দিকে খোলা। গ্রামের খুব সাধারণ পায়খানাটা আমার কাছে কেমন যেন ভয়ানক মনে হলো। টগর বাইরে একা একা দাঁড়াতে ভয় পাচ্ছিল। আমি বুদ্ধি করে দরজা খোলা রেখে পায়খানাতে বসলাম। কিন্তু বসার পরপরই মনে হচ্ছিল কেমন যেন নিস্তব্ধ হয়ে গেছে চারপাশ। দূরে কোথাও যেন একটা পাখি ডেকে উঠল। জঙ্গুলে পরিবেশে এর আগে কোনও দিন, আমি এত রাতে ঘর থেকে বের হইনি।
আমার বুকের ভেতর ঢিপঢিপ করছিল ভয়ে। মনে হচ্ছিল ভয়ে পায়খানা না করেই দৌড় দিই। তবুও মনে মনে সুরা পড়তে পড়তে ধীরে ধীরে বসলাম পায়খানাতে। কিন্তু হঠাৎ করে মনে হলো আমি পানি নিয়ে আসিনি। টগর বাইরেই দাঁড়িয়ে ছিল। ওকে বললাম একটা কিছুতে করে কিছু পানি নিয়ে আসতে। টগর দৌড় দিল শুনেই।
একা একা বসে আছি। মনে হচ্ছে চারপাশে কেমন যেন একটা মরা মরা গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। ছোট বেলায় আমার মন ছিল অনেক কুসংস্কারে পূর্ণ। রাক্ষস খোক্কসের গল্প পড়ে পড়ে মনের ভেতর জন্ম হয়েছিল অন্ধকারের প্রতি নিদারুণ ভয়। আজকে সেটা মনে করে আমার হাসি পায়। কিন্তু সেদিন আমি প্রচণ্ড ভয় পেয়েছিলাম।
খানিক পর টগর পানি আর ল্যাম্প দুই হাতে ধরে নিয়ে এল। আমি এতক্ষণ অন্ধকারে ছিলাম সেটা টগরের হাতে ল্যাম্প দেখে মনে পড়ল। ভালয় ভালয় আমি পায়খানা সেরে যেই বের হতে যাব, এমন সময় আমার পায়ের কাছে কিছু একটা টুপ করে পড়ল। আমি কিছুটা হতচকিত হয়ে গেলাম। প্রথমে শিশির মনে করলেও পরে টগর আমার পায়ের কাছে। ল্যাম্প ধরে দেখে লালচে কিছু একটা। আমি আর টগর প্রায় একসাথে উপরে তাকালাম। দেখি আমাদের ঠিক উপরেই কেউ একজন বসে আছে। দেখেই আমার শরীরে কাঁপুনি ধরে। গেল। ভয়ের চোটে গলা শুকিয়ে গেল। পাশে তাকিয়ে দেখি টগরের গা শক্ত হয়ে গেছে ভয়ে। ভয়ে ভয়ে টগরের হাত থেকে ল্যাম্পটা নিয়ে আমি উপর দিকে ধরলাম। যা দেখলাম তাতে আমার চক্ষু চড়কগাছ হয়ে গেল। লোকটার সারা শরীরে কিছু নেই। মুখ ভর্তি দাড়ি আর গোঁফ। পা ঝুলিয়ে বসে বসে কিছু একটা খাচ্ছে। চেহারা দেখা যাচ্ছে না। শুধু দেখা যাচ্ছে চোখ দুটো। লালচে সাদা চোখ দেখেই আমি চিনে ফেললাম ওকে। সে আর কেউ নয়-আমাদের নিশি মিয়া।
কিন্তু সে এখানে কী করে? এই সব ভাবার আগেই দেখি নিশি মিয়া পেটের খানিকটা নিচের দিক থেকে এক টুকরো মাংস কেটে নিল। তারপর ঘঁাচঘঁাচ করে কেটে খেতে খেতে বলল, খোকা বাবু, কথা দিসিলাম রোগীরে বাঁচাতি না পারলি নিজের মাংস খামু। হের লাইগা তোমাগোরে দেখাইয়া দেখাইয়া খাইতেসি।
বলেই ধারাল কিছু একটা দিয়ে নিজের রান থেকে। গ্র্যাচর্ঘ্যাচ করে এক টুকরো মাংস কেটে খেতে শুরু করল। টপটপ করে রক্ত পড়ে চলেছে। পড়ছে ঠিক আমার সামনে। ভয়ে টগরের দিকে আমার তাকানোর সময় ছিল না। আমি সেখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাই।
পরের দিন আমাদের দুজনকে অজ্ঞান অবস্থায় আম্মা দেখতে পান। পরে আমাদের দুজনকেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অনেক খোঁজ করেও নিশি মিয়ার দেখা পায়নি কেউ। আব্বা অনেক খোঁজ করেছিলেন। কিন্তু পাননি। মাঝে আমিও বড় হয়ে যাই। অনেক দিন কেটে গেছে। আমি হাই স্কুল পাশ করে কলেজে উঠে যাই। দেখতে দেখতে আমি ভার্সিটিতে ভর্তি হই। অনেকগুলো বছর পার হয়ে যায়। আমিও ভুলে যাই নিশি মিয়ার কথা। এখন আমি পড়াশোনার কাজে থিসিসের জন্য এসেছি আমার গ্রামের পাশের গ্রামে। এখানে থাকতে হবে এক বছর। এই এক বছর গ্রামে থেকে গ্রামের মানুষদেরকে নিয়ে থিসিস করতে হবে। দারিদ্র্য বিমোচনের কাজে এইখানে থাকাটা আমার মন্দ লাগছে না। শুধু থাকা-খাওয়াটা একটা সমস্যা। তবে এখানে এখন বেশ কেটে যাচ্ছে সময়।
এই লেখাটা যখন লিখছি তখন অনেক রাত। অমাবস্যা। আকাশে চাঁদ নেই। নেই কোনও মেঘ। চারপাশে ঘুটঘুঁটে অন্ধকার। আমি রাত জেগে পড়াশোনা করি। কিন্তু আজকে আমার মন কিছুটা বিক্ষিপ্ত। গ্রামের চেয়ারম্যান সাহেবের শরীর অনেক খারাপ। ডাক্তার অনেক ট্রিটমেন্ট করেও তাকে ভাল করতে পারেনি। তার পরিবারের লোকজন বলাবলি করছিল অন্য ব্যবস্থা নেবে। ওঁর হার্টের কোনও একটা প্রবলেম। এই সব ভাবতে ভাবতে রাত জেগে থিসিসের কাজ করছি। এমন সময় অনেক দূর থেকে কারও মৃদু চিৎকার শোনা গেল। আমি পড়া ছেড়ে উঠে বাইরে বের হয়ে এলাম। কাউকে দেখতে না পেয়ে ঘরে ঢুকে যাব, এমন সময় অনেক দূরে একটা আগুনের শিখা দেখতে পেলাম। আমার ঘর থেকে সোজা দেখা যায় অনেক দূর। গাছ-পালা কম। অন্ধকারের মাঝেই দেখলাম একটা আগুনের শিখা এগিয়ে আসছে কিছুটা, আবার থামছে। প্রতিটি বাড়ির সামনে থেমে থেমে বাড়ির মানুষের নাম ধরে একবার করে ডেকে ডেকে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। কিছুটা সামনে আসতেই আমি বেশ ভালভাবেই দেখলাম লোকটাকে। মাথায় সেই বিশাল ঝাঁকড়া চুল। মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। আর সেই ভয়ানক দুটো চোখ। একটু ভাল করে লক্ষ করতেই দেখলাম সেই নিশি মিয়া। আমার বাড়ির দিকেই আসছে। নাম ধরে ডেকে চলেছে মানুষকে। যে-ই সাড়া দেবে সে-ই বেঘোরে প্রাণ হারাবে। আরেকটু ভালভাবে দেখতেই দেখি নিশি মিয়ার পেটের ঠিক নিচটায় কেমন যেন খাবলানো। রানের জায়গায় জায়গায় মাংস নেই। কেউ যেন কেটে নিয়ে গেছে সেখানকার মাংসগুলো….
নিতল – রুমানা বৈশাখী
এক
ছেলেবেলায় পানির কাছে যেতে দেখলেই ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসত বুড়ি। নিতল পানি, বাপজান। নামিস না। থাউক, বাপজান, থাউক!
হাজা-মজা পুকুরটার ধারে বসে শ্যাওলা-সবুজ পানির দিকে তাকিয়ে বহুকাল পর বুড়ির জন্যে মনটা কেমন করতে থাকে আজ রাশেদের। দুপুরের রোদ ডানায় মেখে অলস ভঙ্গিতে উড়ে যাচ্ছে কয়েকটা কাক, ছায়ার খোঁজে। আকাশজোড়া রোদরূপী সোনালি আগুন, পুকুরটার চারদিক ঘিরে তপ্ত আলোর আঁকিবুকি করছে। তবুও কিছুতেই বুঝি এতটুকু কাটে না হাজা-মজা পুকুরটার শ্যাওলা-সবুজ পানির অন্ধকার অতলতা। চারপাশের আলোর ছড়াছড়িতে বুঝি আরও বেশি করে আঁধার-কালো মনে হয়।
ছেলেবেলায় বুড়ি কোনওমতেই কখনও নামতে দেয়নি পুকুরের পানিতে। এমনকী বড়বেলায়ও না। ছোট্ট বয়সে অনাথ হওয়া রাশেদের সাত কুলে আপনজন বলতে ওই এক বুড়ি নানিই তো ছিল। বাবা মারা গিয়েছিল জন্মের আগেই, কিছুকাল বাদে নাকি মা-ও। মায়ের চেহারাটা এক বিন্দুও মনে নেই, থাকবার প্রশ্নও ওঠে না। বুদ্ধি হবার পর থেকে এই এক নানিকেই দেখেছে, পরিবার সম্পর্কে যা একটু টুকিটাকি শোনা আছে তার সবটুকুই বুড়ির মুখ থেকে। নানি, রাশেদ আর এই একতলা ঝরঝরে বাড়িটা-এই ছিল এতকাল রাশেদের দুনিয়া।
হ্যাঁ, ছিল। এখন নেই।
গতকাল থেকে বুড়ি নেই জীবনে। আর আগামীকাল থেকে এই অভিশপ্ত বাড়িও থাকবে না। যক্ষ হয়ে আগলে বসেছিল এই বাড়িটাকে বুড়ি। ঢাকা শহরের ওপরে এতখানি জায়গা নিয়ে মাত্র একতলা একটা বাড়ি আর সাথে হাজা-মজা এই পুকুর আগলে বসে থাকার মত বোকামি আর কী হতে পারে? নিজের সামর্থ্য না থাকুক, কোনও রিয়েল এস্টেট কোম্পানিকে দিলেই তো লারে লাপ্পা। নগদ টাকার সাথে তৈরি ফ্ল্যাট গোটা কয়েক, আর কী লাগে জীবন হেসে খেলে পার করতে?
কিন্তু নানিকে এসব বোঝাবে কে? নানির বাবার বাড়ি ছিল এটা, জন্মের পর থেকে এখানেই কেটেছে বুড়ির জীবন। প্রথমে ছিল টিনের ঘর, পরে এই একতলা বাড়ি করেছিলেন। রাশেদের নানাজান। ঘর-জামাই ছিলেন তিনি, খুব সম্ভব স্ত্রীর কারণে হতে বাধ্য হয়েছিলেন। কী বন্ধন যে ছিল এই বাড়ির সাথে নানির, বিয়ের পর স্বামী নিয়েও এই বাড়িতেই থেকে গেছে মৃত্যুর আগের মুহূর্তটা পর্যন্ত। শেষের দিকে তো ঘর থেকেও বেরতে চাইত না, ডাক্তারের কাছে যাবার জন্যেও না। মাঝে মাঝে এসে কেবল বসে থাকত এই হাজা-মজা পুকুরের ক্ষয়ে যাওয়া ঘাটে। বয়স হয়েছিল নব্বই, ছানি পড়া চোখে দেখতে পেতও না ভাল করে। পুকুর পাড়ে বসে নিকষ কালো পানির শরীরে কী দেখার চেষ্টা করত বুড়ি কে জানে। মাঝে তো মনে হত বুঝি বাপের ভিটা নয়, বুড়ির বন্ধন আসলে এই পুকুরটার সাথে।
দুজনের সংসারে উপার্জনক্ষম কেউ ছিল না, কাজেই অর্থ-কষ্ট তো ছিলই বরাবর। একতলা বাড়িটার একটা অংশ ভাড়া দিয়ে চলত সংসার খরচ, আর বিপদে-আপদে হাত দিতে হত নানাজানের রেখে যাওয়া সামান্য কিছু সঞ্চয়ে। বিক্রি না করুক, পুকুরটা ভরাট করে গোটা দুই টিনের ঘর তুললে কিন্তু অনায়াসে আয় বেড়ে দ্বিগুণ হতে পারত। কিন্তু না , বুড়িকে রাজি করাতে পারেনি কিছুতেই। কেন যেন মনে হত, পুকুরটার অস্তিত্বকে কেমন একটু ভয়ই করে বুড়ি।
সে যাই হোক, আজ আর সে নেই। এবং কোনও বাধাও নেই জীবনে। সত্যি বলতে কী, বুড়ির মৃত্যুতে বড় বাঁচা বেঁচে গেছে রাশেদ। মনে-মনে এই একটা কামনাই ছিল যে বুড়ি মরুক, কেননা বুড়ি না মরলে মরতে হত তার নিজেকেই। নানান জায়গায় বিশাল অঙ্কের সব ঋণ জমেছে তার, আর পাওনাদারেরা সব পেশাদার ঋণ ব্যবসায়ী। পাওনা টাকা কী করে উদ্ধার করতে হয় তা ভালই জানা আছে তাদের, সাথে চড়া সুদ আদায়টাও। বুড়ি তো আর বুঝত না যে আজকাল অল্প-বিস্তর নেশাপানি সকলেই করে, না হলে বন্ধু সমাজে ঠিক প্রেস্টিজ থাকে না। আর একটু স্টাইল নিয়ে বাঁচতে, গেলে পকেট গরম না হলে কি চলে নাকি?
ঠিক আছে, ঠিক আছে, রাশেদ না হয় নেশাটা একটু। বেশিই করে। কিন্তু তাতে কী? বন্ধুরাও তো সব করছে, সে-ই বা কেন পিছিয়ে থাকবে? দুই দিনের তারুণ্য, একটু মৌজ মাস্তি করা যেতেই পারে। আজ এ পার্টি, কাল সে পার্টি-সব মিলিয়ে একটা চটকদার জীবনধারার পিছনে খরচ অনেক। আর এই জীবনধারার জন্যেই তো বন্ধুমহলে আজকাল এত জনপ্রিয় সে।
বুড়ি হয়তো বুঝত না তেমন কিছুই, তবে যেটুকুই বুঝত তাতে চোখ রাঙাত বড় বেশি। একদিকে রোজকার ফুর্তির খরচ জোগানো, অন্যদিকে পাওনাদারের ক্রমাগত হুমকি ধমকি, সাথে বুড়ির চোখ রাঙানি-সবমিলিয়ে অসহ্য ঠেকছিল জীবনটা। টাকার অভাবে মেয়েগুলোও একের পর এক হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছিল, অথচ নাকের নিচে পড়ে ছিল অর্থের এত বড় খনি। কতদিন আর সহ্য হয় এসব?
সুতরাং…
রাশেদ তাই করেছে, যা করবার দরকার ছিল নিজের জীবন বাঁচাবার জন্যে। বুড়ির বয়স হয়েছিল, বড় কষ্ট পাচ্ছিল বার্ধক্যের নানান জ্বালায়। রাত হলেই শ্বাসকষ্টে কেঁদে-কেঁদে মত্যকামনা করত সষ্টিকর্তার দরবারে। রাশেদ বেশি কিছু করেনি, সে চাওয়াটাই পূরণ করেছে কেবল। ডাক্তার যে ঘুমের ওষুধ দিতে বলেছিল, সেটার মাত্রাটাকেই কেবল বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে। ব্যস, পরম শান্তিতে মৃত্যুলোকের ওপারে পাড়ি জমিয়েছে বুড়ি।
একে কি খুন বলা যায়?
মোটেই না, অন্তত রাশেদের তা মোটেই মনে হয় না। তবুও আজকের এই রোদজ্বলা অলস দুপুরে পুকুর পাড়ে বসে। বুড়ির জন্যে মনটা কেমন-কেমন করছে। আবার কী মনে করে একটা দীর্ঘশ্বাসও আসে বুক ঠেলে। নিজের জীবন বাঁচাবার জন্যে কতরকমের কাজই না করতে হয় এই জীবনে!
দুই
ঘরে ফিরে নিজের এটা সেটা গোছগাছ করতে শুরু করে রাশেদ একসময়। এতকালের সংসার, তবু নেবার মত বেশি কিছু নেই, নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো কেবল। সত্যি বলতে কী, নিতে চাইলে নেয়া যায় বুঝি অনেক কিছুই। এতকালের সংসার ঠাসা কত শত হরেক রকমের জিনিসপত্রে। তবে বুড়ি নানির কাছে এসবের যতটা মূল্য ছিল, রাশেদের কাছে এখন ততটাই মূল্যহীন। কাল থেকে রাশেদের ঠিকানা হবে গুলশানের একটা ফ্ল্যাটে, বন্ধুদের সাথে স্বপ্নের স্বাধীন জীবনের শুরু। আর নতুন সেই জীবনে এই জরাজীর্ণ পুরানো বাড়ির কিছুই সাথে নিতে চায় না সে। এ দুটো ঢাউস সুটকেসে পরনের জামা-কাপড় আর নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো ধরে যায় সব। টেবিলের এক কোণে পড়ে আছে ভার্সিটির বইপত্রগুলো, সাথে নেবে কি নেবে না ভাবে একবার। শেষে না নেবারই সিদ্ধান্ত নেয়। আগামীকাল কোম্পানির সাথে চুক্তি হবার পর মোটা অর্থের অর্ধেকটা জমা হবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে, আর সেই অর্থের পরিমাণ এতই বিশাল যে এমন বইপত্রের কাড়ি কয়েক লক্ষবার কেনা যাবে অনায়াসে। অযথা টেনে নেয়ার মানে নেই।
বাইরে বেলা পড়ে আসছে ক্রমশ, পুকুরটার চারপাশে আস্তে-আস্তে ঘনাচ্ছে বিকালের ছায়া। জানে না কেন, কাজের ফাঁকেও পোড়ো পুকুরটার অন্ধকারের দিকে নজর যায় বারবার। পুকুরের দিকে, নাকি পুকুর পাড়ে বুড়ির কবরের দিকে? অযথা কবরস্থানের জায়গা কিনে পয়সা নষ্ট করতে চায়নি রাশেদ, বুড়ির এত পছন্দের পুকুর পাড়েই শেষ করেছে। সমাহিত করার কাজ। কিছুদিন পরে এখানে মাথা তুলে দাঁড়াবে বিশাল শপিং মল। না থাকবে এই পুকুর, না থাকবে বুড়ির কবরের চিহ্ন। কিন্তু তাতে কী? রাশেদের মনে হয় না যে সে কোনও অন্যায় করেছে। বুড়ির বাপের ভিটাতেই সমাহিত করেছে দেহ, এবং বুড়ি নানির আত্মা তাতে শান্তি পাবে বলেই মনে হয়।
তবুও বারবার নজর যায় কবর আর পুকুর পাড়ের দিকেই। পোড়ো এই বাড়ির সীমানায় কুকুর-বেড়াল দূরে থাক, এই দিনের বেলাতেও একটা কাক-পক্ষীর সাড়া শব্দ নেই আজ। বুড়ির কটা পুষি বেড়াল ছিল, গতকাল তার। মৃত্যুর পর থেকে সেগুলোও গায়েব। মনে হচ্ছে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে বুঝি। থমথমে, দম বন্ধ করা একটা পরিবেশ। কেমন জানি ভৌতিকও।
নাহ্, আজ রাতটা থাকা যাবে না এখানে। এই পোডড়া বাড়িতে কোনও সুস্থ মানুষ একঘণ্টা থাকলেই পাগল হয়ে যাবে। কী করে যে এতগুলো বছর কাটিয়েছে, তাই এখন বুঝে উঠতে পারে না।
ছপ…ছপ…
মনে হয় কী যেন একটা হেঁটে জানালার ধার দিয়ে গেল। বেড়ালগুলো ফিরে এল কি? মনে-মনে একটু স্বস্তিই লাগে রাশেদের, এতবড় বাড়িতে সে একদম একা নয় ভেবে। এগিয়ে দেখে জানালার ধারে পরম আগ্রহে, তবে চোখে পড়ে না কিছুই। বেড়াল তো, এক জায়গায় বসে থাকার প্রাণী নয়। এতক্ষণে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে বাড়িতে ঢোকার পাঁয়তারা করছে নিশ্চিত।
একটা বাটিতে গরুর দুধ যা আছে, ঢেলে রাখে কেন জানি। আজই তো শেষ, কাল থেকে বেড়ালগুলোরও ঠিকানা বদলে যাবে, আশ্রয় নিতে হবে অলি-গলিতে। শেষমুহূর্তে একটু আহ্লাদ করলে কিছু আসবে যাবে না।
ছপ…ছপ…
এবার শব্দ আসে বসার ঘর থেকে। বেড়ালগুলোই নিশ্চিত। তবে বেড়াল দৌড়ালে ছপছপ আওয়াজ হবে কেন? ভেজা কাপড় পরনে কেউ হাঁটাহাঁটি করলে বরং এমন শব্দ হতে পারে।
একতলা বাড়ি হলেও তেমন অন্ধকার নয়, ভালই আলোর যাওয়া-আসা আছে। তবুও বসার ঘরটা এ মুহূর্তে কেমন অন্ধকারই ঠেকে রাশেদের। আরও অবাক লাগে, যখন দেখতে পায় বসার ঘরের কার্পেটটা ভিজে চুপচুপ করছে। ভিজে আছে সোফা সেটও। বেড়ালগুলোই নিশ্চিত, ভিজে শরীরে জানালা দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়েছে।
কিন্তু প্রশ্ন হলো, বাইরে তো বৃষ্টি-বাদলের চিহ্ন নেই। বেড়ালগুলো ভিজল কী করে? যাই হোক, ফালতু বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় নেই। নিজের ঘরের দিকে রওনা হয় রাশেদ। যাবার সময় চোখে পড়ে বুড়ির ঘরের ভেজানো দরজার গোড়াতেও একরাশ পানি। বেড়ালগুলো তাদের প্রভুকে খুঁজছে বোধহয়।
দেখার আগ্রহ বোধ করে না আর। কোথায় পানি জমল, কোথায় কী নষ্ট হলো এসব নিয়ে মাথা খারাপ করবার সময় কই? কাল থেকে এই বাড়ি, এই বেড়াল, এই পরিবেশ সব ইতিহাস হয়ে যাবে। টুকটাক শখের জিনিসগুলো গুছিয়ে নিলে সময়টা বাঁচবে বরং। সন্ধ্যার আগেই চলে যাবে ঠিক করেছে, অযথা রাত কাটাবার দরকারটাই বা কী? বন্ধু সিয়ামকে বলেছে গাড়ি নিয়ে আসতে, চলে আসবে যে কোনও সময়। রাতে জোস একটা পার্টির পরিকল্পনা আছে উত্তরার দিকে। এখানে একা পচে মরার চাইতে পার্টি করা ঢের ভাল। হাতে এখনও সময় আছে কিছু, আর কাজও প্রায় শেষ। বিছানায় একটু গড়িয়ে নেয়া যেতে পারে, কেননা বাকি রাত তো আর আরাম করার সুযোগ মিলবে না। তা ছাড়া… ছপ..ছপছপছপ…ছপ…
সে আওয়াজ! মনে হয় বুঝি ঘরের ঠিক সামনে দিয়েই হেঁটে যায় কেউ। তাও ভেজা শরীরে একরাশ পানি নিয়ে। চট করেই ঘুরে দাঁড়ায় রাশেদ। কিন্তু নাহ্, কেউ নেই। কীসের না কীসের শব্দ, কোথাও পানি-টানি পড়ছে বোধহয়। গতরাতে বৃষ্টি হয়েছিল, বাড়ির আশপাশে গর্তগুলোতে পানি। জমেছে। সে পানিতে ব্যাঙ লাফাচ্ছে বোধহয়, আর সেই আওয়াজ জানালা দিয়ে আসছে…
হ্যাঁ, তাই হবে। বুঝতে পেরে একটু স্বস্তি লাগে রাশেদের। আসলে হয়েছে কী, বুড়ির মৃত্যুর পর থেকে কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে। গতকালের সকাল-দুপুর তো পার হয়ে গেছে বুড়ির দাফন-কাফন ইত্যাদি করে। আশপাশের প্রতিবেশীরা কেউ কেউ এসেছিল, তারাই সব গুছিয়ে করেছে। রাতেও দূর-সম্পর্কের কয়েকজন আত্মীয় ছিল, বাড়িতে, একা হবার সুযোগ ঘটেনি আর।
কিন্তু সকালের পর থেকে…।
অস্বস্তি অবশ্য হতেই পারে। আর সেটাই স্বাভাবিক। হতে পারে বুড়ির বয়স হয়েছিল, হতে পারে যে বার্ধক্যজনিত কারণে বড় বেশি ভুগছিল, কিন্তু আরও কিছুকাল হয়তো বাঁচত। তারপর আপনা থেকেই আশ্রয় নিত মৃত্যুর কোলে। কিন্তু এটাও ঠিক যে সেই মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছে রাশেদ নিজেই। নিজ হাতে দুধের সাথে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে খাইয়েছে নানিকে। সরল বিশ্বাসে একমাত্র নাতির হাত থেকে গ্লাসের দুধ পান করেছিল বুড়ি।
বড় বৃষ্টি হচ্ছিল সে রাতে এই শহরের বুকে…
তিন
বৃষ্টি মানে রীতিমতন ঝুম বৃষ্টি। রান্নাঘরে যখন কুসুম গরম দুধের গ্লাসে ঘুমের ওষুধগুলো খুঁড়ো করে মেশাচ্ছিল, জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাট এসে ভিজিয়ে দিচ্ছিল বারবার।
চোখে ছানি পড়েছিল শেষকালে, ঠিকমতন দেখতে পেত না নানি। নিজের হাতেই গ্লাসখানা বুড়ির হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল রাশেদ।
এটা খেয়ে শুয়ে পড়ো। অনেক রাত হয়েছে।
মনে কয় না, বাপ। আইজকে খাইয়াম না।
খাবে না মানে কী? রাতে তো কিছু খাও নাই। কলা দিব সাথে?
ফোকলা দাঁতে হাসে বুড়ি পরম মমতায়। ওরে, আমার বাপ রে, মনে কয় না রে দুধ খাইতে।
ডাক্তার বলেছে খেতে। খাও, আরাম হবে। খাও।
ছোট একটা চুমুক দেয় গ্লাসে নানি, আর চিলের মতন প্রখর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে রাশেদ। এই এক গ্লাস দুধ শেষ হবার ওপর নির্ভর করছে তার আগামীকাল। এবং সত্যি বলতে কী, তার জীবনের নিরাপত্তাও। অনেক বুঝিয়েছে বুড়িকে সে, কিন্তু কিছুতেই বাড়ি বিক্রি করে অর্থের সংস্থান করতে রাজি হয়নি বুড়ি। বুড়িকে পরপারে পাঠানোর ব্যবস্থা করা ছাড়া আসলেই কোনও পথ ছিল না সামনে।
ও, নানি, তুমি না একবার এই পুকুরে ডুবে গেছিলে… বহুকালের পুরানো প্রসঙ্গ আবার টেনে তোলে নাতি। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, কথার ছলে দুধটুকু খাইয়ে দেয়া কেবল। বলো না ওই গল্পটা। পানির নিচে কী জানি ছিল?
আলোক আছিল রে। হ্যাঁজাকের বাত্তির মতন আলোক। …তখুন তো এইখানে এত্তবড় দালান আছিল না, আছিল টিনের ঘর। দালান তো অনেক পরে তুর নানাজানে করছে। …আমার বাপজানে বড় শখ কইরে এই পুষুনি কাটায়েছিল একমাত্র কইন্যার জন্যে। আমার বড় হাউশ আছিল পুষুনিতে গোসুল করুম, সাঁতার কাটুম।
তোমার আব্বা তোমাকে অনেক ভালবাসতেন, তাই না?
ওরে, পোলায় কয় কী? আমার বাপজানের জান আছিলাম আমি, বুঝছোস? বাপজান আমার জনমের পর থেইকে নাকি কইত, এই মাইয়া আমি বিয়া দিমু না। ঘরের খুঁটি বানায় রাখুম প্রয়োজনে, তাও বিয়া দিমু না।
এই জন্যে নানাজানকে ঘরজামাই রেখেছিল? টিপ্পনী কাটতে ছাড়ে না নাতি।
ধুরো, হারামজাদা। তুর নানাজানে তো ঘরজামাই আছিল আমার কারণে। পীর সাহেবে কইছিল এই ভিটার থেইকে আমারে পৃথক না করতে, পুস্কুনি থেইকে পৃথক না করতে। হেই কারণে তো নানাজানে এই ভিটায় আছিল। তুর নানাজানে কি আর শখ কইরে থাকত নাকি…
নানাজানের গল্প বাদ। তুমি পুকুরে ডোবার গল্পটা বলো তো। আর দুধটা খাচ্ছ না কেন? খেতে খেতে গল্প বলো… তাড়া দেয় রাশেদ।
অগত্যা দুধের গ্লাসে আবার চুমুক।
আমার বয়স তখন বারো, বুঝছোস? ডাঙর হইছি, এইদিক-ওইদিক থেইকে বিয়ার প্রস্তাব আসে। মাথায় অনেক লম্বা চুল আছিল, ওই চুলের জইন্যেই আসত বিয়ার প্রস্তাব। একদিন হইছে কী জানোস, পুষুনির ঘাটে বইসে চুলে তেল দিতেছি…হঠাৎ দেখি সামনে ইয়া বড় এক সাপ। মাগো মা, কী সেই সাপ! ফণা তুইলে বইসে আছে সামনে। বাড়ির দুয়ার থেইকে আম্মাও দেখছে সেই সাপ, আর সাথে সাথে তো দিছে চিক্কুর। বাপজান আছিল না বাড়িত, আমি আর আম্মায় শুধু…হইল কী, চিকুরের সাথে-সাথেই সাপে দিল ছোবল। আমার আর তারপরে কিছু মনে নাই।
তুমি তো পুকুরে পড়ে গেছিলে, নাকি?
সেইটাও আমার মনে নাই রে, বাপ। আম্মার কাছে শুনছি যা শুনার। আম্মায় বলছে সাপে কাটার সাথে-সাথে নাকি আমি তো অজ্ঞান। ছিলাম পুষুনির ঘাটে, অজ্ঞান হইয়ে। সোজা গিয়া পড়লাম পানিতে। আর তলায় গেলাম। আম্মা একলা মেয়েমানুষ কী করবে? খালি চিক্কর দিতেছিল। লোকজন জড় হইয়ে খুঁজাখুঁজি কইরে শেষমেশ দুইঘণ্টা পরে পাওয়া গেছিল নাকি আমারে।
মনে মনে হাসে রাশেদ। আদ্যিকালের মানুষের এই হলো এক ব্যাপার, সবকিছু বাড়িয়ে বলবে। পাঁচ-দশ মিনিটকে বাড়িয়ে বলছে দুই ঘণ্টা। দুই ঘণ্টা পানির নিচে থাকলে কি মানুষ বাঁচে নাকি? তাও যে মানুষকে সাপে কেটেছে। ঘণ্টা দুয়েকের মাঝে তো সাপের বিষেই মরে যাবার কথা।
…পানির থেইকে তোলার পরে তো আরেক কাহিনি, বুঝছোস? সকলে তো ভাবছে আমি বাইচে নাই, এত সময় পানির তলে থাইকে তো আর মানুষ বাঁচে না। পানি থেইকে তোলার পরে তো দেখা গেল আমি নিঃশ্বাস নেই না। আমি পষ্ট দেখছি যে আমারে সাপে কাটছে। আমি একা না, আম্মাও দেখছে। পানির থেকে তোলার পরে দেখা গেল কোথাও সাপে কাটার চিহ্নও নাই। ওঝা ডাকছিল বাপজান। বিষ ঝাড়নের জইন্যে। ওঝায় কইছিল, শরীলে বিষের কুনো বালাই নাই। আমারে নাকি সাপেই কাটে নাই কুনোদিন..
কণ্ঠস্বরটা স্তিমিত হতে-হতে নিভে যায় একসময়, বর্ষণের প্রচণ্ড আওয়াজের সাথে মিলেমিশে যায় বুঝি। জানালার ধারে দাঁড়ানো রাশেদ একবার ফিরে তাকাবারও প্রয়োজন বোধ করে না, কেননা জানা আছে তার কী ঘটছে। সামনে এখন অনেক কাজ-লোকজন ডাকা, নানির দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি ইত্যাদি। ঠাণ্ডা মাথায় সেই সব পরিকল্পনাই করেছে বরং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।
একটু ভাল করে ভাবলেই রাশেদ হয়তো বুঝতে পারত যে ছেলেবেলা থেকে শুনে আসা এই গল্পের মাঝে অন্যরকম কী যেন একটা আছে। বুঝতে পারত যে রূপকথার গল্প মনে করে যে গল্প এতকাল জেনে এসেছে, সেটা গল্প না হয়ে সত্যিও হতে পারে!
চার
সেদিন বোঝেনি, বিশ্বাস করেনি।
বিশ্বাস আজও করে না। তবুও আজ এই একলা বাড়িতে কেমন যেন খটকা লেগেই থাকে মনে। বাইরে সূর্য ডুবেছে অনেকক্ষণ, দিনের শেষ চিহ্নগুলোও মিলিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে। চার দেয়ালের এই ঘেরাটোপে আস্তে আস্তে নেমে আসতে শুরু করেছে অন্ধকার ছায়া।
ভীষণ অস্থির লাগে, ছটফট লাগে মনের মাঝে। নাহ্, আর দেরি করা যাচ্ছে না। বন্ধুরা আসুক বা না আসুক, বেরিয়ে পড়বে এখন। প্রয়োজনে বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে, কিন্তু এই সীমানার মাঝে না। অস্থিরতায় দম বন্ধ হয়ে মরতে হবে নইলে।
সুটকেস দুটো টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসে বাইরে। কী মনে করে দরজায় তালা আঁটে, মেইন গেটের তালার চাবিটাও নেয় সাথে। দুনিয়ার লোকজনকে বিশ্বাস নেই, রাতারাতি পরের বাড়ি দখল হয়ে যায় আজকাল। শহরে গৃহহীন মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে…
এ কী! এমন লাগছে কেন?
শ্বাসটা কেমন বন্ধ হয়ে আসছে, বুঝি হঠাৎ করে অক্সিজেনের ঘাটতি পড়েছে সৃষ্টিকর্তার দুনিয়ার বুকে…উফ!
কী কষ্ট!! কী কষ্ট!!
মুখ খুলে প্রাণপণে শ্বাস নিতে চেষ্টা করে, আর বুঝতে পারে যে কঠিন দুটো হাত পেছন থেকে চেপে ধরেছে গলা। সাঁড়াশির মতন শক্ত দশটি আঙুল চেপে বসেছে গলার ওপরে। শীতল…হিমশীতল দুটো হাত।
মৃত মানুষের মতন শীতল! আর ভেজা!
প্রাণ বাঁচাবার ভীষণ তাগিদে নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে রাশেদ। নিজেকে নিয়োগ করে নিজেকেই বাঁচাবার কাজে। অন্ধকার হয়ে আসছে চোখের সামনে দুনিয়াটা ক্রমশ, একটু বাতাস পাওয়ার আকুতিতে ছটফট করছে বুকের খাঁচায় ফুসফুস। এখনই…আর কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র! এর মাঝে যদি নিজেকে মুক্ত করতে না পারে, তো জীবনের এটাই শেষ দৃশ্য।
আহ!
নিজেকে কোনওমতে সাঁড়াশি আঙুলগুলো থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে প্রাণপণে অক্সিজেন টানে রাশেদ। শান্তি…শান্তি…
কিন্তু এর পরে যা দেখতে পায়, তাতে জমাট কংক্রিট হয়ে যায় বুকের রক্ত। এই তো…এই তো একটু দূরেই দাঁড়িয়ে আছে সে। চিকন পাড়ের সাদা শাড়ি পরা জবুথুবু এক বুড়ি, সন্ধ্যার অন্ধকারের মাঝেও যার চোখজোড়া ধকধক করছে অপার্থিব হিংস্রতায়। এটা কী করে হয়? মৃত মানুষ জীবিত হয় কী করে?
কী করে হয়?
না-না, বুড়ি জীবিত নয়। হতে পারে না। কিছুতেই না! নিজের অজান্তে পেছাতে শুরু করে রাশেদ একটু একটু করে। আর এক পা এক পা করে এগোয় বুড়ি। ভিজে চপচপ করছে। পুরো শরীরটা তার, একটি একটি পদক্ষেপের সাথে শব্দ তোলে পরনের ভেজা শাড়ি…ছপ-ছপ-ছপ…ছপছপ-ছপ।
হাতদুটো সামনে বাড়ানো, ফোকলা মুখে কুৎসিত হাসি হাসছে প্রেতাত্মা। এবং রাশেদ জানে…জানে যে এই হাতদুটো তাকে ধরেই ফেলবে। চেপে ধরবে তার গলা, আর ধরেই থাকবে যতক্ষণ না প্রাণবায়ু বেরিয়ে যায়।
কী যে হয়ে যায়, শরীর-মনের সমস্ত সাহস একত্রিত করে। ঘুরে দাঁড়ায় রাশেদ, আর খিচে দেয় দৌড়।
কিন্তু…
শরীর সামনে বাড়ে না এতটুকুও। কেননা পেছন থেকে চেপে ধরেছে সেই সাঁড়াশি আঙুলগুলো আবার। হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে রাশেদ, দুহাতে সর্বোচ্চ জোর প্রয়োগ করে ছাড়া পেতে চায় সেই মরণ-বাঁধন থেকে।
লাভ হয় না কোনও। জীর্ণ-শীর্ণ সেই হাত মাটিতে ঘষটে-ঘষটে নিয়ে যেতে থাকে ছাব্বিশ বছরের তরতাজা যুবক রাশেদকে। টেনে নিয়ে যেতে থাকে অমোঘ সেই। নিয়তির দিকে..
যে নিয়তি সে নিজ হাতে নিজের জীবনের ললাটে লিখেছে।
পাঁচ
কীভাবে এরপর কী হলো, জানে না রাশেদ। শুধু অনুভব করে…
অনুভব করে যে একরাশ কালো শীতল জল প্রবল শক্তিতে টেনে নিচ্ছে তাকে। টেনে নিচ্ছে অতল গহ্বরে। শরীরের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে প্রবেশ করছে অপার্থিব সেই পানি। বুক পর্যন্ত পৌঁছে গেছে পানি। তারপর প্রবেশ করছে চোখের পাতায়, নাসারন্ধ্রে, কানের গহ্বরে…আর…
শীতল হয়ে আসছে চারপাশ ক্রমশ।
পরিশিষ্ট
দেয়াল টপকে ভেতরে ঢুকে পড়বে কি না ঠিক বুঝতে পারে না রতন।
বেশ অনেক মাস যাবৎ দেখছে বাড়িটায় লোকজনের আনাগোনা নেই। রাতে বাতি-টাতিও জ্বলে না। এক বুড়ি আর বুড়ির নাতি থাকত এখানে। বুড়িটা তো মাস তিন-চার আগেই মরেছে, নাতিটাও বোধকরি থাকে না আর। অবশ্য এই ভাঙাচোরা শ্যাওলা ধরা বাড়িতে কেই-বা থাকতে চাইবে।
যাই হোক, যা আছে কপালে, রাত হয়েছে, আশপাশে লোকজন নেই। সুযোগ বুঝে তাই ভেতরে ঢুকেই পড়ে রতন। যা পাওয়া যায়, তাই লাভ। স্টিলের বাসনপত্র পেলেও লাভ আছে। আজকাল চোরা বাজারে সবই বিকোয়। পেশায় সে ছ্যাচড়া চোর, শ পাঁচেক টাকার মাল-সামান পেলেও আজকে রাতের মত খুশি।
নাহ, কেউ নেই। পুরো বাড়ি ঘুটঘুঁটে অন্ধকার। সাথে টর্চ নেই, থাকলে ভাল হত। অন্ধকারে চোখটা সয়ে গেলে আয়েসী ভঙ্গিতে এগোয় রতন। এঘর-ওঘর ঘুরেফিরে দেখে। কিছু বাসনপত্র পায়, বস্তায় ভরে। কিছু বিছানার চাদর, ক জোড়া জুতো, দামি কিছু ইংরেজি বইপত্র, আরও টুকটাক নানান জিনিস। যা পায়, বস্তায় ভরার যোগ্য হলে ভরে ফেলে।
একে তো নড়বড়ে শ্যাওলা ধরা পুরানো বাড়ি, তার ওপরে মেঝে থইথই করছে পানিতে। পানির কারণে বহু কিছুই পচে গলে গেছে। অনেকদিন যাবৎ বুঝি জমে আছে পানি, বোটকা একটা পচা গন্ধ আসছে। পানির উৎস কোথায় বুঝতে পারে না রতন। অবশ্য বোঝার চেষ্টাও করে না। নাক চেপে কোনওমতে ঘরগুলোতে সন্ধান করে মূল্যবান কিছুর।
বাকি কেবল একটা ঘর। ওটা দেখা হলেই সোজা বাউণ্ডারির বাইরে। কেমন গা ছমছম করছে এই কালি গোলা অন্ধকারে। বের হয়ে খোলা বাতাসে শ্বাস নিতে না পারলে জানে মারা পড়বে।
করিডরের একদম শেষমাথায় ঘরটা। অন্ধকার বুঝি এখানে আরও বেশি জমাট। আর শীতল। ঘরের দরজাটা ভেজানো।
ধাক্কা দিতেই কাঁচকোচ আওয়াজে খুলে যেতে শুরু করে দরজাটা। আস্তে…খুব আস্তে! দৌড় দেবে কি না বুঝতে পারে রতন। কেননা এই ঘুটঘুঁটে অন্ধকারের মাঝে পষ্ট দেখতে পায় বিছানায় বসে আছে এক বুড়ি, আর তার পায়ের কাছে একটা পুরুষ কাঠামো। বসে আছে, পিছন ফিরে।
এ কি সেই বুড়ি না? ওই যে বুড়িটা মারা গেল কয়মাস আগে…মানে কী? মানে কী এসবের? এই বুড়ি তো মরেছে, নিজের চোখে লাশ দেখেছে রতন।
বুড়িটা নামে বিছানা থেকে। ধীরে, খুব ধীরে। নিচু কণ্ঠে কী যেন বলে বিড়বিড়িয়ে। অস্পষ্ট, এলোমেলো। ভয় নাই, ব্যাটা…এরপরে আর কুনো ভয় থাকব না…কুনো ভয় নাই… শান্তি…শান্তি…
পরনের প্যান্টটা কখন ভিজে গেছে ভয়ে টেরও পায় না রতন। চিৎকার করে প্রাণপণে, কিন্তু গলা দিয়ে বেরয় না, আওয়াজ। কারণ…
একজোড়া জীর্ণ-শীর্ণ বুড়ো মানুষের হাত কণ্ঠরোধ করে দিয়েছে রতনের।
সাঁড়াশির মত শক্ত একজোড়া হাত!
আগমন – নাজনীন রহমান
গ্রামের মানুষ ভীষণ ভয় পায় ভূত-প্রেতে, ওদের ধারণা অশুভ, খারাপ জিনিস মিশে থাকে বাতাসে, তারপর সুযোগ মত মানুষের ঘাড়ে চাপে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন সাধারণ মানুষ মন। থেকে দূর করতে পারে না ভীতি। গ্রামে বেল গাছ, ঘন বাঁশ ঝাড়, শেওড়া গাছ, গাব গাছের অভাব নেই-সবার বদ্ধমূল ধারণা, এসব গাছ ভূত-পেত্নিদের খুবই প্রিয়, তাই নানা খারাপ জিনিস এই গাছগুলোতে থাকে।
এমনই এক গ্রামে বাস করে সচ্ছল কৃষক রমিজ আলী। তার দুই ছেলে রতন ও মণি।
রতন বিয়ে করেছে, দুই বছরের ফুটফুটে সুন্দর একটা ছেলে আছে তার।
রমিজ এখন বৃদ্ধ হয়েছে, শরীরে শক্তি-সামর্থ্য কিছুই নেই, রতনই বাবার সম্পত্তির দেখভাল করে। বিশ্বস্ত-কর্মঠ কামলা, মজুর আছে-অসুবিধে হয় না।
মণি বৈষয়িক কাজে নেই, তার ভাল লাগে নদীতে ঝাপাঝাপি করে মাছ ধরতে, গাছে উঠে ফল পাড়তে, সঙ্গী সাথী নিয়ে হৈ-হুঁল্লোড় ও গল্প-গুজব করতে। রমিজ রাগ করেছে, হ্যাঁ রে, এইভাবে গায়ে বাতাস দিয়া কদ্দিন চলবি? বড় ভাইটা একলা খাইট্টা শেষ হইল, অরে সাহায্য করা লাগে না? আর কিছু না করিস, শাক-সবজির চালান নিয়া শহরে তো যাইতে পারিস?
আমার ওসব ভাল লাগে না, বলে নির্বিকারভাবে সরে পড়ে মণি।
মণির সর্বক্ষণের সাথী হলো রাজু, একেবারে ছোট থেকে আছে সে এই বাড়িতে। এতিম ছেলেটাকে রাস্তা থেকে তুলে এনেছিল রমিজ, তারপর বাড়ির ছেলের মতই হয়ে গেছে সে। রতন আর মণি গ্রামের স্কুলে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছে, তারপর, পড়াশোনা করতে ইচ্ছে হয়নি বলে স্কুল বাদ দিয়ে রতন বাবার কাজে সাহায্য করেছে।
আর মণি?
মনের সুখে দুষ্টুমি করে বেড়িয়েছে। কোন্ গাছের ডালে পাখির ছানা আছে, কার গাছের ফল পেকেছে, এসবে সে পুরোপুরি হাফেজ। আর রাজু তো মণির অন্ধ চামচা। দুজনে। ঘুমায়ও এক ঘরে, মণি চৌকিতে আর কাছেই মাটিতে বিছানা করে শোয় রাজু। ঘুমাবার আগে কত গল্প হয় দুজনার।
রতনদের ধান-চাল, নানা ফল, সবজির ব্যবসা-বিশাল কারবার। মণি বাউণ্ডুলের মত ঘুরে বেড়ায়, বাবার সেটা একদম সহ্য হয় না। দুই ভাই মিলেমিশে কাজ-কর্ম করবে, এটাই রমিজের মনের ইচ্ছে। বকাবকি, শাসন করেও কোনও লাভ হয় না। মণি তার ইচ্ছেমতই যা খুশি করে বেড়ায়। রতন খুবই ভালবাসে ছোট ভাইকে, বাবাকে বোঝায়, থাক, বাপজান, ওরে কিছু বইলো না, আমি তো আছিই, হেসেখেলে চলুক কিছুদিন, দেইখো সব ঠিক হইয়া যাইব।
রাজু খুব হাসি-খুশি-রসিক ছেলে, সে-ও সেদিন গম্ভীর মুখে মণিকে বলল, ছোট ভাই, আপনে একটা বিয়া কইরা ফালান, তাইলে বাজান বউয়ের সামনে আপনারে বকতে পারব না।
রাগ করতে গিয়েও হেসে ফেলল মণি, বলল, ফাজিল ছোকরা, তুই বিয়া কর, খুব শখ-না?
মুখটা করুণ করে রাজু বলল, আমারে মাইয়া দিব কেডা? একদিন সালাম চাচার মাইয়ারে একটা গোলাপ ফুল দিছিলাম। গালি তো যা দিবার দিলই, শ্যাষে স্যাণ্ডেল ছুঁইড়া মারল।
হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে গেল মণির।
আস্তে আস্তে কাজ শুরু করল মণি। করতেই হলো। বিরাট কারবার তাদের, অনেক টাকা-পয়সার ব্যাপার। রতন একা সবদিক সামলাতে পারে না, কর্মচারী থাকলেও নিজেদের খেয়াল রাখা দরকার। মণি আর গাফিলতি করল না, ভাইকে সাহায্য করতে লাগল। শহরে চালান নিয়ে যায়, কখনও ধান, চাল, শাক, সবজি, কখনও ফল। রাতের বেলায় ট্রাক নিয়ে রওনা হয়, ভোরে কাজ শেষ করে ফিরে আসে। রাজুকে সঙ্গে নেয়, সেজন্য খারাপ লাগে না, বরং প্রতিটি ট্রিপ বেশ উপভোগ্য হয়।
মাঘ মাস, শীতকালীন সবজি দিয়ে ভরা হয়েছে ট্রাক। তিনজন শ্রমিক নিয়ে রওনা হলো মণি। আজ আর রাজু সঙ্গে নেই। জ্বর হয়েছে ওর। সবজির যাতে ক্ষতি না হয়, সেভাবে ব্যবস্থা করে শ্রমিকরা গরম কাপড় মুড়ি দিয়ে গুটিসুটি হয়ে ট্রাকের খোলা জায়গায় শুলো। মণিও ওদের একপাশে শুয়ে পড়ল। ড্রাইভার বলল, ভাইজান, আপনে বাইরে কষ্ট করবেন ক্যান? ঠাণ্ডা লাগব, ভিতরে আসেন।
মণি রাজি হলো না। ওদের ঠাণ্ডায় কষ্ট হবে, আর আমি আরামে থাকব? তা হয় না। ভাল করে শরীর ঢেকে নিল মণি।
রাস্তায় তেমন যানবাহন নেই, ড্রাইভার গতি বাড়িয়ে গন্তব্যে ছুটে চলল। এসব রাস্তায় বাতির ব্যবস্থা নেই, অন্যান্য গাড়ির হেডলাইটে চারদিক মাঝে-মাঝে আলোকিত হচ্ছে। নিকষ কালো অন্ধকার ভীতিকর করে তুলেছে শীতের রাতকে। আজ ঠাণ্ডাটা খুব বেশি। মণি যতই শরীর ঢেকে শুয়েছে, তারপরও ঠাণ্ডায় জমে যাবার অবস্থা হলো। ঠাণ্ডার চোটে একসময় ভেঙে গেল ঘুমটা ওর। ভাবল, ট্রাকের ক্যাবে চলে যাবে? অন্যদের দিকে তাকিয়ে দেখল, দিব্যি ঘুমাচ্ছে। ওরা। খেটে খাওয়া মানুষ, তাপ কিংবা ঠাণ্ডা ওদেরকে কাবু করতে পারে না।
কম্বলটা ভাল করে গায়ে টেনে নিয়ে ঘুমাবার চেষ্টা করল মণি। প্রায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, সেই অবস্থায় হঠাৎ ওর মনে হলো কী যেন অসঙ্গতি আছে ট্রাকে। পূর্ণ সজাগ হয়ে উঠল সে, অন্ধকারে অত ভাল দেখা যায় না, তারপরও মণি বুঝল শেষ শ্রমিকটার পাশেই আরও একজন শুয়ে আছে।
কী ব্যাপার?
শ্রমিক ছিল তিনজন, চারজন হলো কেমন করে?
একেবারে ট্রাকের শেষদিকে শুয়ে আছে মানুষটা। চলন্ত ট্রাকে কেউ উঠবে, তা-ও অসম্ভব। রাজুই কি শেষ মুহূর্তে ওদেরকে ফাঁকি দিয়ে উঠেছিল? তা-ই বা কী করে হয়! ট্রাক ছাড়ার পরও তো তিনজন শ্রমিকই ছিল। তা হলে? শরীরটা কেমন ছমছম করে উঠল মণির। ভয় পেলেও সাহস সঞ্চয় করে বলল, কে রে ওখানে? রাজু নাকি?
ভারী জান্তব এক স্বর শোনা গেল, না, আমি রাজ নই
তারপরই মণির ভয়ার্ত চোখের সামনে ধীরে ধীরে যে উঠে বসল, মানুষ নয় ওটা, ভয়াল এক পিশাচ! রাতের অন্ধকারে, অশুভক্ষণে শিকারের সন্ধানে ঘুরছে সে, আজ সুযোগ পেয়েই ট্রাকে চলে এসেছে।
শয়তানটার কালো কুচকুচে চিকন, রোমশ শরীর। অন্ধকারে দুটুকরো অঙ্গারের মত জ্বলছে চোখ দুটো। কুৎসিত মুখে সাদা চোখাচোখা দাঁত বের করে বীভৎসভাবে হেসে উঠল বিভীষিকাটা, তারপর লিকলিকে কালো হাত দুটো লম্বা হতে হতে পেঁচিয়ে ধরল মণির গলা। বরফ-শীতল সেই হাতের স্পর্শে থরথর করে কেঁপে উঠল মণি। সাপের মত ঘিনঘিনে পিচ্ছিল গা।
চিৎকার করতে পারল না মণি, দম বন্ধ হয়ে আসছে। ঘৃণিত রোমশ হাতের ছোঁয়ায়। পাশে যে শ্রমিক শুয়ে আছে, তাকে ধাক্কা দিয়ে ওঠাবার শক্তিও পেল না।
পিশাচটা শ্রমিকদের ওপর দিয়ে ভেসে এসে আষ্টেপৃষ্ঠে মণিকে পেঁচিয়ে ধরে গলায় বসিয়ে দিল ধারাল দাঁত। দুচোখ আঁধার হয়ে এল মণির। তারপরই জ্ঞান হারাল। এতবড় ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটল টেরও পেল না শ্রমিকরা, জানতে পারল না হেলপার-ড্রাইভারও।
ড্রাইভার তো একমনে গাড়ি চালাচ্ছে, সমস্ত মনোযোগ সামনের রাস্তায়।
এক সময় নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে থামল ট্রাক।
মাল খালাস করছে শ্রমিকরা, গম্ভীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মণি, কথায় কথায় একে-ওকে ধমক দিচ্ছে। তুচ্ছ ব্যাপারে বিশ্রী গালাগালি করছে। সবাই খুব অবাক হয়ে গেল, হাসিখুশি মানুষটার আজ হলো কী? অন্যদিন কত কথা বলে, তামাশায় মেতে ওঠে, সবাইকে চা-নাস্তা খাওয়ায়। অথচ এখন? সম্পূর্ণ অন্য মানুষ, ভয়ে কাছেই যাওয়া যাচ্ছে না। _ ওই রাতের ঘটনার পর খুব দ্রুত বদলে যেতে লাগল মণি। কাজে যায় না, অন্ধকার ঘরের কোণে চুপচাপ বসে থাকে। কী হয়েছে জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয় না, ছেড়ে দিয়েছে খাওয়া-দাওয়া। চিন্তিত হয়ে পড়ল বাড়ির সবাই। রতন ডাক্তার দেখাবার কথা বলল, কিন্তু মার ধারণা অন্য: রাত-বিরাতে যাওয়া-আসা করেছে, খারাপ বাতাস লেগেছে। বুঝি! ভাল হয় ইমাম সাহেবকে দিয়ে দোয়া পড়ালে।
ওই কথা শুনে ঘরের মধ্য থেকেই গর্জে উঠল মণি, আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না, একলা থাকতে দাও আমাকে।
রাজু, যে অত প্রাণের দোস্ত ছিল, তার সাথেও কথা বলে না মণি। রাতে শুয়ে এখনও রাজু নানারকম কথা তোলে, কিন্তু কোনও জবাব পায় না। অনেক অনুনয় করে বলেছে রাজু, ছোট ভাই, আপনের কী হইছে, আমারে বলেন, আমি কাউরে বলুম না।
ভয়াল স্বরে জবাব দিয়েছে মণি, আমারে বিরক্ত করলে তোর খবর আছে।
আজকাল মণিকে ভয় পায় রাজু।
ছোট ভাই আর আগের মত নেই, কেমন করে তাকায়, চেহারাতেও পরিবর্তন হয়েছে। মোমের মত সাদা, তেলতেলে
অদ্ভুত ভাব মুখে, শরীরটা কেমন কালো হয়ে গেছে।
সবচেয়ে আশ্চর্য কথা, একেবারে না খেয়ে সে আছে। কীভাবে?
শরীরও দিব্যি সতেজ ও সবল।
এ কী রহস্য?
কেউ ভেবে পায় না মণিকে নিয়ে কী করবে।
কিছুদিন পর, এক রাতে ভেঙে যায় রাজুর ঘুম। বাথরুমে যাবে। মণির বিছানায় চোখ পড়ে। নেই সে, এত রাতে গেল। কোথায়? বাথরুমে? রাজু নিঃশব্দে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বাথরুম দেখল। খালি, কেউ নেই। সদর দরজায় নজর পড়তেই চমকে উঠল রাজু। দরজা খুলে বেরিয়ে যাচ্ছে মণি।
রাজু সাহসী ছেলে, ভয়-ভীতি কমই তার। ভাবল, এত রাতে ছোট ভাই কই যায়? অবশ্য একটা ব্যাপার রাজুকে একটু অস্বস্তিতে ফেলল। মণি খুব লম্বা নয়, কিন্তু সামনে যে রয়েছে, সে অসম্ভব লম্বা, বড়সড় গাছের সমান প্রায়। এবার একটু ভয় পেলেও চুপিসারে মণির পিছু নিল রাজু। ভয়ের চাইতে কৌতূহলই বেশি, তাকে দেখতেই হবে, ছোট ভাই কোথায় যায়।
গ্রামের পাশেই কবরস্থান। বড় বড় গাছপালায় ঘেরা জায়গাটায় দিনের বেলায় যেতেই মানুষ ভয় পায়, আর এই অন্ধকার রাতে কবরস্থানেই গিয়ে ঢুকল মণি!
বুক ঢিবঢিব করছে, গা ছমছম, তবু একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি দিল রাজু। কবরস্থানে মণি কী করবে, দেখবে সে। না দেখলেই বোধহয় ভাল ছিল। মণি কবর খুঁড়ে লাশ বের করে আয়েশ করে খাচ্ছে!
ভয়ে গায়ের সমস্ত রোম দাঁড়িয়ে গেল রাজুর। কীভাবে ঘরে ফিরল, বলতে পারবে না। বেহুশের মত বিছানায় পড়ে রইল সে।
সকাল হতেই হুঁশ ফিরল রাজুর। সভয়ে দেখল, মণি তার বিছানায় ঘুমাচ্ছে, ঘরের মধ্যে বিশ্রী দুর্গন্ধ। রাতের কথা মনে হতেই গা গুলিয়ে বমি এসে গেল রাজুর। কোনওমতে বেরিয়ে এসে পুকুরপাড়ে গলগল করে বমি করে ফেলল, তারপর ভাল করে হাত-মুখ ধুয়ে ঘাটেই বসল। ঘরে যাওয়ার সাহস হলো না।
সুস্থির হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে লাগল। কাল রাতে যাকে দেখেছে, সে মণি হতে পারে না। গ্রামের ছেলে, ভূত-পেত্নির ব্যাপার জানা আছে রাজুর। সে ঠিকই বুঝল, মণির ওপর খারাপ জিনিস ভর করেছে। কখন কোথায় ধরল ছোট ভাইকে? মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল ওর। কাঁদতে লাগল, ওর এত ভাল ভাইটার এই পরিণতি হলো? এ রাজু যেমন সাহসী, তেমনি বুদ্ধিমানও। বুঝতে পারল, এই নিয়ে এখনি হৈ-চৈ করলে সর্বনাশ হবে। মণি যদি টের পায় যে তার গোমর ফাঁস হয়ে গেছে, তা হলে সবাইকে মেরে ফেলবে সে।
খুব গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল রাজু।
অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা কাকে বলা যায়?
বড় ভাইকে বললে তো সে হাউমাউ করে উঠবে।
এমন কাউকে বলতে হবে, যে এই বিপদ থেকে তাদের রক্ষা করতে পারবে।
এরপরেই তার মাথায় এল: বাড়িতে হাঁস-মুরগির অভাব নেই, রোজই একটা-দুটো করে গায়েব হয়ে যায়। সবাই ভাবে, শিয়ালে নিয়ে যায়। তা হলে এই ব্যাপার? এসব পচা লাশ, কাঁচা মাংস, অখাদ্য, কুখাদ্য খেয়েই ছোট ভাই তরতাজা থাকে, ভাবতেই বমি বমি লাগল রাজুর।
সেদিন থেকে রাজু ভাবতে লাগল, কী করা যায়?
যা করার জলদি করতে হবে।
রাজু আর মণির ঘরে শোয় না, অন্য কামলাদের সাথে ঘুমায়। একটা ভূতের সাথে ঘুমাবার সাহস তার নেই।
হঠাৎ তার মাথায় বুদ্ধি এল: আরে, এই কথাটা সে ভাবেনি কেন? মসজিদের ইমাম সাহেবকে তো বলা উচিত ছিল! একমাত্র তিনিই যোগ্য লোক, যিনি এই ভয়াবহ বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারবেন তাদেরকে। আর দেরি না করে মসজিদে গিয়ে ইমাম সাহেবকে সব খুলে বলল রাজু।
শুনে তিনি বললেন, আমাকে দেখাতে পারিস?
সেদিন রাতেই মণির লাশ খাওয়ার দৃশ্য দেখলেন ইমাম সাহেব। রাজুকে বকলেন, হতভাগা, আমারে আরও আগে বলতে পারিস নাই? এ তো সর্বনাশা এক পিশাচের পাল্লায় পড়েছে মণি! জলদি এর একটা বিহিত না করলে আস্ত গ্রাম বিপদে পড়বে। রতনকে এবার জানাতেই হবে।
সে রাতেই ইমাম সাহেব গিয়ে সব খুলে বলতে কান্নাকাটি শুরু করল রতন, ভয়াল প্রেতের পাল্লায় পড়েছে। আদরের ছোট ভাই?
ইমাম সাহেব বললেন, মনকে শক্ত করো, বাবা। এখন কান্নার সময় নয়, দিনের বেলা অশুভ জিনিসের শক্তি থাকে না। সুতরাং যা করবার দিনের বেলায়ই করতে হবে। আর কাউকে কিছু বলার দরকার নাই, তোমার মা-বাবারে তো বলবাই না। আমি কাল সকালেই তোমাদের বাসায় যাব। খুব সাবধান, মণি যেন কিছু টের না পায়। রাতে ও যা খুশি করুক, বাধা দিতে যেয়ো না, ওর সামনেই থাকবা না কেউ তোমরা।
রাতের অশুভ অন্ধকার দূর হয়ে ভোর হলো। সূর্যের আলো ঝলমল করছে।
ইমাম সাহেব এলেন, মণি তখনও অন্ধকার ঘরে ঘুমে বিভোর।
প্রথমে পুরো বাড়িতে দোয়া পড়া পানি ছিটালেন ইমাম সাহেব, তারপর কয়েকজন শক্তিশালী কামলাকে নির্দেশ দিলেন ঘর থেকে মণিকে বের করতে।
বাইরে নিয়ে এসে শক্ত একটা বাঁশের খুঁটির সঙ্গে বাঁধা হলো মণিকে।
সমানে, দোয়া পড়ে চলেছেন ইমাম সাহেব, এরমধ্যে জেনে গেছে পুরো গ্রামের লোকজন। সবাই এসে জড় হয়েছে। রতনদের উঠানে, অবশ্যই মণির কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রেখে।
ততক্ষণে ছুটে এসেছে রতন-মণির মা-বাবা।
বিষয়টা কী? মা চিৎকার করে উঠল, আমার পোলারে বাইন্ধা রাখছ ক্যান! কী করছে সে?
মণির সর্বনাশের কথা রতনের কাছে শুনল মা-বাবা।
মা পাগলের মত হাহাকার করে উঠল, আমার এমুন, লক্ষ্মী পোলা, তার এই অবস্থা হতে পারে না, তোমরা মিথ্যা বলছ।
ইমাম সাহেবের ইশারায় রতনের বউ জড়িয়ে ধরে ঘরে নিয়ে গেল মাকে।
মণি তার রক্ত-লাল চোখ মেলে, মুখে ফেনা তুলে গালাগালি দিতে লাগল, তারপর রাজুর দিকে তাকিয়ে কুৎসিত মুখভঙ্গি করে ভয়াবহ স্বরে বলল, আমি জানি, তুই-ই আমারে ধরাইয়া দিছিস! তোরে আমি ছাড়ম না! তোর হাড় মাংস চিবাইয়া খামু!
ভয়ের চোটে মুহূর্তে ওখান থেকে গায়েব হয়ে গেল রাজু।
গর্জে উঠলেন ইমাম সাহেব, চুপ থাক, শয়তানের বাচ্চা, তোর শয়তানি আমি বাইর করতাছি, ব্যাটা ইবলিস।
কাজ শুরু করলেন ইমাম সাহেব। শুকনো মরিচ পুড়িয়ে, মাটির বাসনে আরও নানা উপকরণ সাজিয়ে মণির মুখের সামনে ধরলেন। জিনিসগুলোর ঝাঁঝাল ধোঁয়া ওর নাকে-মুখে প্রবেশ করতে লাগল। সেই সাথে দরাজ কণ্ঠে জোরে জোরে দোয়া পড়ে ফুঁ দিতে লাগলেন মণির শরীরে। তারপর হুঙ্কার দিয়ে বললেন, কে তুই? এরে ধরলি কোথায়?
বলুম না। কিছু বলুম না।
রেগে গিয়ে দুজন কামলাকে হুকুম দিলেন ইমাম সাহেব, যেন মোটা দুই বাঁশ দিয়ে মারতে শুরু করে।
নিজে দোয়ার জোর আরও বাড়িয়ে দিলেন।
যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মণিরূপী পিশাচ কাতর স্বরে বলল, আমি কে, জানতে চাইস না। এক আন্ধার রাইতে খোলা ট্রাকে এই ব্যাটারে ধরছি।
ইমাম সাহেব দ্বিগুণ রেগে গিয়ে বললেন, জানি, তুই একটা বদ, হারামি পিশাচ! ট্রাকে তো আরও মানুষ ছিল, ওদের কাউরে ধরলি না ক্যান?
ভয়াল হেসে পিশাচ্ বলল, দূর-দূর, চিমড়া কামলাদের শরীরে আছে নাহি কিছু? এই ব্যাটা হইল দুধ-ঘি খাওয়া টসটসা জিনিস-শরীল ভরা তাজা মিঠা রক্ত, তাই এরেই ধরছি।
ইমাম সাহেব বললেন, অহন এরে ছাড়বি নাকি বল? না ছাড়লে তোর আরও খারাবি আছে, কইয়া দিলাম।
ওরে ছাইড়া কোনও লাভ হইব না, শরীলের সব রক্ত খাইয়া শ্যাষ কইরা, ব্যাটারে তো সেইদিনই মাইরা ফালাইছি। অহন আমি ছাড়লেই লাশ হইয়া যাইব।
শুনে থমকে গেলেন ইমাম সাহেব, দুঃখ হলো তাঁর মণির জন্য। চিৎকার করে উঠলেন, বেশ করছিস, খবিসের পুত। বাইর হইয়া যা জলদি।
গোঁয়ারের মত পিশাচটা বলতে লাগল, কতদিন পর একটা শরীল পাইছি, ছাড়ম না অরে।
ইমাম সাহেব তখন শুকনো একটা গাছের শিকড় বের করে ওটাতে আগুন ধরালেন, তারপর পিশাচটার নাকের কাছে ধরে সমানে দোয়া পড়তে লাগলেন।
এইবার কাবু হলো পিশাচ, চেঁচাতে লাগল সমানে, যাইতাছি, যাইতাছি, সরা ওইটা। ১ গম্ভীর হয়ে বললেন ইমাম সাহেব, দূর হ, হারামজাদা, আর কোনওদিন যেন এই গ্রামে তোরে না দেহি।
তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মণির নাক-মুখ দিয়ে বের হতে লাগল কালো ঘন ধোয়া।
ইমাম সাহেবের শক্তিশালী দোয়ার জোরে ধোয়াটা দ্রুত সরে যেতে লাগল। তারপর আর দেখাই গেল না। পরিষ্কার নীল আকাশ, কোথাও কোনও কালিমা নেই, অশুভ ছায়ামুক্ত প্রকৃতি।
সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।
নিষ্প্রাণ মণি বাঁশের খুঁটিতে বাঁধা। মাথা ঝুলে পড়েছে। বুকের ওপর। বিশ্রী দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। কতদিনের বাসি মড়া।
রতনদের বাড়িতে নেমে এল শোকের ছায়া।
রমিজ আলী মাথায় হাত দিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। মনে পড়ল কত বকাবকি করেছে ছেলেটাকে। দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগল তার।
মণির মা তো পাগলের মত হয়ে গেল।
এরপর থেকে দিন-রাত কাঁদতে লাগল মণির মা। আকুল হয়ে ডাকত: বাজান, আমার বাজান, কই গেলি? ফিরে আয়, ফিরে আয় রে!
রতনের অবস্থা দারুণ শোচনীয়। ছোট ভাইটাকে হারিয়ে সে-ও পাগলের মত হয়ে গেছে।
মণি নেই, এই সত্যিটা মেনে নিতে পারছে না কেউ।
কিন্তু সময় সব কিছু ভুলিয়ে দেয় মানুষকে।
দিন থেমে থাকে না।
প্রকৃতি তার আপন নিয়মে চলতে থাকে।
রাজুর মনের দুঃখও একসময় কমল। ছোট ভাইয়ের মুখটা ভাল করে মনে পড়ত না। আগের চাইতেও বেশি কাজ করতে লাগল সে, যাতে কোনওমতেই তার প্রিয় মানুষটার কথা মনে না পড়ে।
রতনের ফুটফুটে নাদুস-নুদুস বাচ্চাটা রাজুর খুব ন্যাওটা, ওর কাছেই বেশিরভাগ সময় থাকে সে।
রাজুও খুব আদর করে বাচ্চাটাকে।
একদিন সকালে বাচ্চাটাকে আর পাওয়া গেল না।
রতন সেদিন বাসায় ছিল না, মাল নিয়ে শহরে গেছে। বউ একাই ছিল ঘরে। ভোরে ঘুম ভাঙতেই দেখল বাচ্চা নেই। ঘরের দরজা খোলা। তার চিৎকারে ছুটে এল সবাই।
অনেক খোঁজাখুঁজির পর বাঁশঝাড়ের মধ্যে পাওয়া গেল। বাচ্চাটাকে। অক্ষত নয়, রক্তাক্ত মাথাটা শুধু পড়ে আছে। বন্ধ দরজা খুলে বাচ্চাটাকে বাইরে নিয়ে গেল কে, কেউ বুঝল না। আরও একবার শোকের মাতম উঠল গ্রামে।
ভূত-পিশাচ মানুষ নয় যে, তাদের অনুভূতি, বিবেক, নীতি থাকবে।
রাজু যে এখন স্বাভাবিক খাবার খায় না, সেটা কেউ খেয়াল করেনি। রাতের আঁধারে সে যায় কবরস্থানে। কবর থেকে তুলে খায় পচা লাশ। হাঁস-মুরগির কাঁচা মাংস তৃপ্তি করে পেটে পুরছে। এবং সে-ই চিবিয়ে খেয়ে নিয়েছে রতনের তুলতুলে নিষ্পাপ বাচ্চাটাকে।
রাজুর উপর ভর করেছে সেই ভয়ঙ্কর পিশাচ।
ইমাম সাহেবকে দেয়া কথা রাখার প্রয়োজন মনে করেনি, ফিরে এসেছে আবারও।
তা ছাড়া, রাজুর ওপর তার আক্রোশ ছিল।
রাজুকে তো বটেই, পুরো গ্রামকে সে ধ্বংস করবে।
ঠিক করেছে এরপর শেষ করবে ইমাম সাহেবকে।
এক সকালে দেখা গেল, তার ঘরে মরে পড়ে আছেন। ইমাম সাহেব।
কোনও এক অসতর্ক মুহূর্তে পিশাচটা মেরে ফেলেছে। তাঁকে।
গ্রামবাসী জানে না, তাদের জন্য অপেক্ষা করছে কী ভয়ঙ্কর বিপদ।
মসজিদে ইমাম সাহেব না থাকলে কি চলে?
নতুন ইমাম সাহেবের জন্য আহ্বান করা হয়েছে।
গ্রামবাসী তারই অপেক্ষা করছে।
ভয়াবহ অশুভ থেকে গ্রামকে রক্ষা করতে পারবেন নতুন ইমাম সাহেব?
পঞ্চবক্র তান্ত্রিক – আফজাল হোসেন
এক
ঝড়-বৃষ্টির রাত।
জয়নাল হ্যারিকেনের আলোতে বই পড়ছে। তাদের গ্রামে এখনও ইলেকট্রিসিটি এসে পৌঁছয়নি। প্রায় দশ বছর আগে ইলেকট্রিক লাইন টানার খুঁটি পোঁতা হয়েছিল। খুঁটি পোঁতা পর্যন্তই, লাইন টানা আর হয়ে ওঠেনি। গ্রামের মানুষ অপেক্ষায় আছে নিশ্চয়ই কোনও এক দিন খুঁটিতে লাইন টানা হবে, আর তারাও আলোর মুখ দেখতে পাবে।
জয়নাল হাজী মোঃ আবুল কালাম ডিগ্রি কলেজের ছাত্র। এ বছর সে ডিগ্রি পরীক্ষা দিচ্ছে। কাল ইংরেজি পরীক্ষা। ইংরেজিতেই তার যত ভয়। তার ধারণা, যদি সে ডিগ্রিতে ফেল করে এক মাত্র ইংরেজিতেই ফেল করবে।
রাত পৌনে একটার মত বাজে। ঘুমে জয়নালের চোখ বুজে আসছে। বার-বার হাই উঠছে। এর পরও পড়া চালিয়ে যাচ্ছে। আরও আধ ঘণ্টার মত পড়ার পরে বিছানায় যাবে।
জয়নালের মা নেই। ওর জন্মের পরপরই মা মারা যান। কোনও ভাই-বোনও নেই। আপনজন বলতে আছেন শুধু। বাবা। বাবাই তাকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছেন। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আর বিয়ে থা-ও করেননি। তিনি রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। যা রোজগার করেন তাতে তাদের বাপ-ছেলের সংসার খেয়ে-পরে ভালই চলছে।
জয়নালের বাবা অনেক আগেই ঘুমিয়েছেন। আকাশের মেঘ ডাকার শব্দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গুড়-গুড় করে নাক ডেকে তিনি ঘুমাচ্ছেন। সারা দিনে অনেক পরিশ্রম করতে হয় তাকে। এক দিকে যেমন বাইরে রাজমিস্ত্রির কাজ করেন, তেমন ঘরে ফিরে রান্না-বান্না সহ যাবতীয় সাংসারিক কাজ সারতে হয়। জয়নালকে কোনও কাজেই হাত লাগাতে দেন না। তার শুধু একটাই চাওয়া, জয়নাল যেন লেখা-পড়া শিখে মানুষের মত মানুষ হয়। বড় চাকরি করে। তার মত হাড় ভাঙা খাটুনি যেন জয়নালকে করতে না হয়।
জয়নাল তার বাবার ইচ্ছে পূরণের যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। সারাক্ষণ পড়াশোনা নিয়েই থাকে। বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আড্ডা মেরে, চায়ের দোকানে বা অন্য কোথাও সময় কাটানো, অথবা টিভি দেখে বা কোনও খেলা নিয়ে মেতে থেকে সময় নষ্ট করে না। অত্যন্ত নিরীহ-ভদ্র-লাজুক প্রকৃতির ছেলে। প্রয়োজন ছাড়া ঘরের বাইরেও বেরোয় না। গ্রামের সবাই তাকে ভাল ছেলে হিসেবেই চেনে।
পড়তে-পড়তে হঠাৎ জয়নাল অনুভব করল কেমন একটা অদ্ভুত বিদঘুঁটে গন্ধ পাচ্ছে নাকে। যেন ইঁদুর মরা গন্ধের সঙ্গে মুর্দার আতরের গন্ধের মিশেল।
জয়নাল বসার ঘরের খোলা জানালার সামনে টেবিলে বসে পড়ছে। খোলা জানালা দিয়ে হু-হুঁ করে বৃষ্টি ভেজা ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। সে মাথা তুলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। বাড়ির সামনের ছোট্ট উঠনটা দেখা যাচ্ছে। ঘন-ঘন বিজলি চমকানোর আলোতে উঠনে জমে থাকা বৃষ্টির পানি ঝিকমিক করছে। উঠনের এক পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ঝাকড়া আম গাছটাও দেখা যাচ্ছে। দমকা হাওয়া ভেজা আম গাছটার ডাল-পালায় আলোড়ন সৃষ্টি করছে।
জয়নাল আবার পড়ায় মন দিল। ভাবল, দমকা হাওয়ার তোড়ে দূরে কোথাও থেকে হয়তো ওই বিদঘুঁটে গন্ধটা ভেসে এসেছে। কিছুক্ষণ পরেই ওটা আর পাওয়া যাবে না।
খানিকবাদে লক্ষ করল গন্ধটা আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। যেন গন্ধের উৎস আশপাশেই রয়েছে। চোখ তুলে আবার জানালার দিকে তাকাল। জানালায় চোখ পড়তেই ভীষণ চমকে উঠল। জানালার শিক ধরে অদ্ভুত ভয়ানক চেহারার এক লোক দাঁড়িয়ে রয়েছেন।
লোকটা একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে আছেন। ডাকাতের মত বড়-বড় লাল চোখ জোড়ায় ভয়ানক অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। মুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল। মাথায় জটা ধরা লম্বা চুল। গায়ে কালো রঙের আলখিল্লা। গলায় কয়েক ধরনের মালা। রুদ্রাক্ষের, গাছের শিকড়-বাকড়ের, প্রাণীর হাড়-গোড়ের, পাখির পালকের, তাবিজের আর টকটকে লাল জবা ফুলের মালা। কাঁধে কাপড়ের পুঁটলি। হাতে ধরা সাপের মত একটা আঁকা-বাঁকা লাঠি।
ওই লোকটার গা থেকেই ভর-ভর করে সেই বিদঘুঁটে ঘ্রাণটা আসছে। গন্ধে জয়নালের কেমন মাথা ঝিমঝিম করছে।
লোকটাকে দেখে জয়নাল এতটাই চমকে গেছে যে তার মুখে কথা ফুটতেই বেশ সময় লাগল।
কে আপনি?
লোকটা কোনও জবাব দিলেন না। পলকহীন জয়নালের দিকে তাকিয়েই রইলেন।
জয়নাল আবার জিজ্ঞেস করল, কে আপনি? এত রাতে কোথা থেকে এসেছেন? কী চান?
এবারে লোকটা কথা বলে উঠলেন। গমগমে গলায় ধমকের সুরে বললেন, আমি তোকে চাই। চল আমার সঙ্গে। আমি তোকে নিতে এসেছি।
জয়নাল অবাক গলায় বলল, কে আপনি?! আমাকে নিতে এসেছেন মানে?!।
লোকটা গলার স্বর উঁচিয়ে বললেন, আমি তান্ত্রিক পঞ্চবক্র। সময় নষ্ট না করে চল আমার সঙ্গে, চল। তোকে আমার খুব প্রয়োজন।
জয়নাল বলল, না, আমি আপনার সঙ্গে যাব না। চিনি না, জানি না, কেন যাব আপনার সঙ্গে?!
লোকটা প্রায় হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, বেয়াদব! আমার কথা না শুনলে তোর অনেক বিপদ হবে। তুই সব হারাবি!
জয়নাল কিছুটা চটা গলায় বলল, চিৎকার করছেন কেন? আস্তে কথা বলুন। আমার বাবা ঘুমাচ্ছেন। তার ঘুম ভেঙে যাবে। রাস্তার পাগল কোথাকার!
লোকটা মেঘের গর্জনের মত গলায় বলে উঠলেন, তুই আমাকে রাস্তার পাগল ভাবছিস?! আমি তান্ত্রিক পঞ্চবক্র। আমার ক্ষমতা সম্পর্কে তোর কোনও ধারণাই নেই।
জয়নাল বলল, রাস্তা-ঘাটে পীর-ফকির, সাধু-ওঝা তান্ত্রিকের ভেক ধরা আধ পাগল অনেককেই দেখা যায়। তাই বলে এই মাঝ রাতে আপনি কোথা থেকে এসেছেন?!
লোকটা গর্জে উঠলেন, তুই আমাকে ভণ্ড ভাবছিস! তার মানে তুই আমার সঙ্গে যাবি না?
ভণ্ড না ভেবে সত্যিকারের তান্ত্রিক ভাবলেও যেতাম না। এত রাতে বাবাকে না বলে অচেনা কারও সঙ্গে কোথাও যাওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না!
লোকটা ঠোঁটের কোনায় তির্যক হাসি ফুটিয়ে বললেন, তোর বাবা যদি তোকে ফেলে কোথাও চলে যায়?
জয়নাল আঁতকে উঠে বলল, না, আমার বাবা আমাকে ফেলে কোনও দিনও কোথাও যাবেন না।
লোকটা বললেন, আমার সঙ্গে না গিয়ে বিরাট ভুল করলি। অনেক বড় মাশুল দিতে হবে তোকে। চলে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বললেন, আবার আমি তোকে নিতে আসব। সেদিন তুই স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে যেতে চাইবি।
লোকটা হাতে ধরা লাঠিতে ভর দিয়ে খালি পায়ে উঠনের কাদা-পানির মধ্যে পা ফেলে-ফেলে যেতে লাগলেন। জয়নাল। তাঁর গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইল। এখনও বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। সেই সঙ্গে বিজলি চমকাচ্ছে। সারা রাতই বোধহয়। এমন বৃষ্টি হবে।
কী আশ্চর্য! জয়নাল অবাক-বিস্মিত চোখে দেখতে পেল, বৃষ্টিতে লোকটার গা ভিজছে না। তার চলার পথের বৃষ্টি থেমে যাচ্ছে।
জয়নাল বিস্ফারিত চোখে চেয়েই রয়েছে। লোকটা বাড়ির সীমানা পেরিয়ে রাস্তায় নেমেছেন। বসার ঘরের এই জানালা দিয়ে রাস্তাটা অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়।
হঠাৎ তীব্র নীলচে আলোর ঝলকানিতে বিজলি চমকের সঙ্গে কান ফাটানো বিকট শব্দে বাজ পড়ল। সেই সঙ্গে অদ্ভুত লোকটাও গায়েব হয়ে গেলেন। অথচ তার আগমুহূর্তেও থেমে-থেমে বিজলি চমকানোর আলোতে লোকটাকে দেখা যাচ্ছিল। যেন কোনও অদৃশ্য শক্তি বজ্রপাতের তীব্র আলোর ঝলকানিতে লোকটাকে দৃশ্যপট থেকে মুছে ফেলেছে।
দুই
সকালে ঘুম ভেঙে জয়নাল, নিজেকে টেবিলে বইয়ের উপর মাথা রাখা অবস্থায় পেল। তার মানে গত রাতে সে পড়তে পড়তে টেবিলে মাথা রেখেই ঘুমিয়ে পড়েছিল।
আড়মোড়া ভেঙে সোজা হয়ে বসল জয়নাল। গত রাতের অদ্ভুত লোকটার কথা মনে পড়ল। লোকটা চলে যাবার পরপরই বোধহয় সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সে দ্বিধায় পড়ে গেল, সত্যিই কি সেই লোকটা এসেছিলেন? নাকি টেবিলে মাথা রেখে ঘুমের মাঝে স্বপ্নে দেখেছে?
ঝড়-বৃষ্টির রাতের পর রৌদ্রোজ্জ্বল ঝকঝকে সকাল। জয়নালের বাবা খুব ভোরেই ঘুম থেকে উঠেছিলেন। তিনি সকালের রান্না সেরে ফেলেছেন। আজ রান্না করেছেন মোটা চালের ভাত, শুকনো মরিচ দিয়ে করা লালচে রঙের আলু ভর্তা, ধনে পাতা দেয়া ডিম ভাজি, চিংড়ী মাছ দিয়ে কলমি শাক আর কলাই ডালের চচ্চড়ি।
প্রতিদিনই জয়নাল জেগে ওঠার আগেই তিনি সকালের রান্নার কাজ সেরে ফেলেন। জয়নাল জেগে উঠলে একসঙ্গে খেয়ে কাজের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। টিফিন ক্যারিয়ারে করে সকালের রান্না খাবার থেকে কিছু খাবার দুপুরে খাওয়ার জন্যও নিয়ে যান। বাকি খাবার থেকে যায় দুপুরে জয়নালের খাওয়ার জন্য। সন্ধ্যায় কাজ থেকে ফিরে আবার রাতের খাবার রান্না করেন। এভাবেই চলছে তাদের বাপ-ছেলের সংসার।
বাবা-ছেলে একসঙ্গে সকালের খাওয়া সেরে দুজনেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। জয়নাল যাচ্ছে পরীক্ষা দিতে। সকাল নটায় পরীক্ষা শুরু হবে। তার আগেই তাকে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছতে হবে।
জয়নালের বাবা যাচ্ছেন তাঁর কাজের সাইটে। তারও সকাল নটার মধ্যে পৌঁছতে হবে। আজ একটা পাঁচতলা বিল্ডিঙের ছাদ ঢালাইয়ের কাজ করবেন।
.
পরীক্ষা শেষে জয়নাল হল থেকে বেরিয়েছে। বেশ ভাল হয়েছে পরীক্ষা। ইংরেজি নিয়ে অনেক ভয় ছিল তার মনে। এখন মনে হচ্ছে ভয়ের কিছু নেই। ইংরেজিতে সে ষাটের উপরে নম্বর পাবে। বাকি পরীক্ষাগুলো আশানুরূপ হলে এস.এস.সি-এইচ.এস.সি-র মত ডিগ্রিতেও সে ফাস্ট ডিভিশন পাবে।
পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে বাইরে বেরিয়ে জয়নাল তার চাচাকে দেখতে পেল। জয়নালের বাবার এক মাত্র বড় ভাই বেলায়েত হোসেন। তাঁর মুখ অসম্ভব রকমের ভার। চেহারা কেমন। বিধ্বস্ত। চোখ-মুখ লাল আর ফোলা-ফোলা।
এ জয়নাল তার চাচার দিকে এগিয়ে গিয়ে অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল, চাচাজান, আপনি এখানে?
বেলায়েত হোসেন থমথমে গলায় বললেন, তোকে নিতে এসেছি।
জয়নাল আশ্চর্য হওয়া গলায় বলল, আমাকে নিতে এসেছেন মানে?! শঙ্কিত গলায় আরও যোগ করল, বাড়িতে কোনও সমস্যা হয়েছে নাকি?
বেলায়েত হোসেন বুজে আসা গলায় বললেন, তোর বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।
জয়নাল ব্যাকুল গলায় বলে উঠল, বাবা অসুস্থ! কী হয়েছে তাঁর?! সকালে তো দুজন একসঙ্গেই বাড়ি থেকে বেরোলাম। তিনি চলে গেলেন তাঁর কাজের সাইটে। কী হলো বাবার?!
বেলায়েত হোসেন ভারাক্রান্ত গলায় বললেন, চল, বাড়িতে গিয়েই দেখতে পাবি।
জয়নাল চাচার সঙ্গে রিকশা করে বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিল। ওর মনের ভিতর তোলপাড় হয়ে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই তার বাবার সাংঘাতিক কিছু হয়েছে। চাচাজান তাকে সব বলছেন না। কিছু একটা লুকাচ্ছেন।
জয়নাল তাদের বাড়ির সামনে পৌঁছে দেখতে পেল উঠনে অনেক লোকের ভিড়। রিকশা থেকে নেমেই সে ছুটে চলে গেল বাড়ির দিকে। তাকে ছুটে আসতে দেখে লোকজন দুপাশে সরে তার যাওয়ার জায়গা করে দিয়েছে।
উঠনের মাঝখানে চাটাইয়ের উপর কে যেন শুয়ে রয়েছে। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা। সমস্ত চাদরটা ছোপ-ছোপ রক্তে মাখা। জয়নাল সেখানে গিয়ে থামল।কেউ একজন শোয়ানো লোকটার মুখের উপর থেকে চাদর সরাল। রক্ত মাখা একটা মুখ দেখা গেল। জয়নালের বাবার মুখ। নিথর পড়ে আছেন। জয়নালের বুঝতে দেরি হলো না তার বাবা মারা গেছেন।
আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে চিৎকার করে জয়নাল কাঁদতে শুরু করল। ওর কান্নায় আশপাশের পরিবেশ ভারী হয়ে উঠল।
জয়নালের বাবা মারা গেছেন পাঁচতলা বিল্ডিঙের ছাদ ঢালাইয়ের সময় ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে। তবে তাঁর পড়ে যাওয়াটা বেশ রহস্যজনক। তিনি এমনি-এমনি পড়ে যাননি। ছাদ ঢালাইয়ের মাঝে হঠাৎ কালো রঙের একটা চিল এসে তাঁর উপর চড়াও হয়। আরও অনেকেই সেখানে ছিল, কিন্তু তাদের সবাইকে ছেড়ে চিলটা শুধু ওর বাবাকেই লক্ষ্য বানায়। চিলটা উড়ে-উড়ে এসে ছোঁ মেরে ওর বাবার মুখে মাথায় আঁচড়-খামচি আর ঠোকর বসাতে থাকে। হঠাৎ অতর্কিত হামলায় তিনি দিগ্বিদিজ্ঞান হারিয়ে ছাদের কিনারে চলে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে যান।
.
আসরের নামাজের পর জয়নালের বাবার জানাজা হয়েছে। এখন কবরস্থানে নিয়ে গিয়ে কবর দেয়া হচ্ছে। জয়নাল কেঁদে-কেঁদে আকুল। তার দুই চাচাতো ভাই আর চাচা মিলে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছে। কিছুতেই যেন জয়নালের চোখের পানি আটকানো যাচ্ছে না।
কবরটা পুরোপুরি মাটি চাপা দিতে দিতে সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। ততক্ষণে লাশের সঙ্গে আসা লোকেরা প্রায় সবাই-ই চলে গেছে। শুধু জয়নাল, তার দুই চাচাতো ভাই, চাচা আর দুই গোরখোদক আছে। হঠাৎ জয়নালের চোখ পড়ল কবরস্থানের উত্তর মাথায়। সেখানে বেশ মোটা একটা রেইনট্রি গাছ রয়েছে। গাছটার আড়াল থেকে কে যেন তাদেরকে লক্ষ করছে। লোকটার গায়ে কালো পোশাক।
এক পর্যায়ে লোকটার মুখ দেখতে পেল জয়নাল। গত রাতের সেই অদ্ভুত লোকটা। লোকটা সোজা তাকিয়ে রয়েছেন জয়নালের দিকে। তার ঠোঁটের কোণে তির্যক হাসি।
জয়নাল তার চাচা আর চাচাতো ভাইদেরকে লোকটার কথা জানাল। চাচা বেলায়েত হোসেন অবাক গলায় বললেন, কোথায়?! কে আমাদের লুকিয়ে দেখছে?
জয়নাল আঙুল তুলে রেইনট্রি গাছটার দিকে দেখাল।
চাচা, চাচার দুই ছেলে সহ গোরখোদকরাও সেদিকে তাকাল। নাহ, কাউকেই তারা দেখতে পেল না। তবে কুচকুচে কালো রঙের একটা কুকুর দেখতে পেল সবাই।
বেলায়েত হোসেন বললেন, ওখানে তো একটা কুকুর। মনে হয় লাশের গন্ধে এসেছে। গোরখোদকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, ভালভাবে মাটি চাপা দিয়ে। শেয়াল-কুকুর যেন কিছুতেই মাটি সরিয়ে লাশের নাগাল না পায়।
জয়নাল দেখল তার চাচা ঠিক কথাই বলছেন। সত্যিই রেইনট্রি গাছটার ওখানে একটা কুকুর। সেই অদ্ভুত লোকটা নয়। তা হলে কি এতক্ষণ সে চোখে ধাঁধা দেখেছে?
তিন
জয়নাল নিজেদের বাড়ি ছেড়ে চাচার বাড়িতে উঠেছে। চাচাই তাকে তার বাড়িতে নিয়ে এসেছেন। বাবাকে হারিয়ে জয়নালের পক্ষে পুরো একটা বাড়িতে একা থাকা সম্ভব নয়। তার উপর এখনও পরীক্ষা শেষ হয়নি। তাই চাচা চাইছেন তাঁর কাছে থেকে জয়নাল যাতে বাকি পরীক্ষাগুলো নির্বিঘ্নে দিতে পারে। তা ছাড়া এই মুহূর্তে জয়নালকে একা রাখাটা কিছুতেই ঠিক হবে না। তাতে একা-একা বাবার কথা মনে করে আরও বেশি কান্নাকাটি করবে।
চাচার স্ত্রী মারা গেছেন বহু বছর আগেই। চাচার সংসার তাঁর দুই ছেলেকে নিয়ে। বড় ছেলে স-মিলে কাজ করে। জয়নালেরই সমবয়সী ছোট ছেলের গ্রামের বাজারে চায়ের দোকান রয়েছে। চাচা তার বড় ছেলেকে বিয়ে করাতে চাইছেন। পছন্দসই মেয়ে পাচ্ছেন না বলে বিয়ে করানো হচ্ছে না।
চাচার সংসারে জয়নালের দিন ভালই কাটছে। চাচার দুই ছেলেই সারা দিন বাইরে কাটায়। শুধু দুপুরের খাওয়ার সময় তারা এসে খেয়ে যায়। চাচা বাড়িতেই থাকেন। তার দুটো দুধেল গাভী আছে। তিনি ঘরের রান্না-বান্না আর গাভী দুটোর দেখ-ভাল নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। জয়নালকে বিছানা, আলনা, পড়ার টেবিল সহ আলাদা ঘর দেয়া হয়েছে। চাচা এবং দুই চাচাতো ভাইয়ের কথা হচ্ছে কিছুতেই যেন জয়নালের পড়ায় কোনও ব্যাঘাত না ঘটে
জয়নাল তাদের বংশের গর্ব। যে করেই হোক জয়নালকে পড়াশোনা শেষ করে ওর বাবার। ইচ্ছে পূরণ করতে হবে। বাবার কাছে জয়নাল যেভাবে আদরে ছিল, বলা যায় চাচার কাছেও সেভাবে সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে।
.
মাঝ রাত। জয়নালের ঘুম ভেঙে গেছে।
সে আবার সেই অদ্ভুত লোকটাকে দেখেছে। ঠিক ধরতে পারছে না, সে কি স্বপ্নে নোকটার দেখা পেয়েছে, নাকি সত্যিই লোকটা এসেছিলেন?
সে ঘুমন্ত অবস্থায় ছিল। হঠাৎ সেই রাতের মত নাকে বিশ্রী গন্ধ পায়। ইঁদুর মরা দুর্গন্ধের সঙ্গে মুর্দার আতরের গন্ধের মিশেল। এক সময় অনুভব করে তার মাথার কাছে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। যে এসেছে তার গা থেকে লালচে আলোর দ্যুতি বেরোচ্ছে। অন্ধকার ঘর লালচে আভায় ভরে গেছে।
গমগমে গলার স্বর শোনা যায়, তোর বাবা পৃথিবী থেকে, চলে গেছেন, এখনও তুই আমার কথা শুনবি না?
জয়নাল ভীত গলায় বলে ওঠে, কে আপনি?
আমি তান্ত্রিক পঞ্চবক্র।
আপনি আবার এসেছেন?
হ্যাঁ, তোকে নিতে এসেছি।
আপনার সঙ্গে আমি কেন যাব? কী চান আমার কাছে?
শুধু তোকে চাই। বিনিময়ে তুই কী চাস বল? ধন সম্পদ-ক্ষমতা এমনকী পরমায়ু-সব আমি তোকে দিতে পারব।
আপনার কাছে কোনও কিছুই চাই না আমি। শুধু আপনার সঙ্গে যেতে চাই না।
আবার ভুল করবি? বাবাকে তো হারালি, আরও কত হারাতে চাস?
বাবার কথা ওঠায় জয়নালের মনটা ভীষণ কেঁদে উঠল। অসহিষ্ণু গলায় বলল, আপনি আমার কাছ থেকে চলে যান। চলে যান বলছি।
ঠিক তখন জয়নাল নিজেকে ফিরে পেল। যেন স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙেছে। সমস্ত গা ঘামে ভিজে গেছে। কেউ নেই তার মাথার কাছে। নেই লালচে আভা। অন্ধকার ঘর। তবে বিশ্রী গন্ধটা তখনও পাওয়া যাচ্ছে।
জয়নাল বিছানা থেকে উঠে এক গ্লাস পানি পান করে আবার শুয়ে পড়ল।
.
সকালে চিৎকার-চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙল জয়নালের। আওয়াজটা আসছে বাইরে থেকে।
জয়নাল ঝট করে বিছানা থেকে নেমে বাইরে বেরোল। বাইরে তার দুই চাচাতো ভাই তাদের বাবাকে পাজাকোলা করে গোয়াল ঘরের দিক থেকে নিয়ে আসতে-আসতে সাহায্যের জন্য চিৎকার করে সবাইকে ডাকছে।
জয়নালও ছুটে গিয়ে চাচাকে ধরল।
চাচাকে সাপে কেটেছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে তিনি গোয়াল ঘরে গিয়েছিলেন গরু দুটোকে খড় কেটে দিতে। সেখানে কুচকুচে কালো রঙের একটা সাপ তাকে ছোবল মেরে পালিয়ে যায়। তাঁর আর্তচিৎকারে প্রথমে চাচাতো ভাইদের একজন ছুটে যায়। সেই ভাইয়ের চিৎকার শুনে অন্য ভাইটিও জেগে উঠে ছুটে যায়। ততক্ষণে তিনি একেবারে ঢলে পড়েন। সমস্ত শরীর নীলচে রঙ ধারণ করেছে। মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে।
মুহূর্তেই আশপাশের বাড়ির লোকজন জড় হয়ে যায়। একজন চলে যায় সাপের ওঝা ডেকে আনতে। কিন্তু ওঝা আসার আগেই তিনি মারা যান।
চার
মাঝ রাত। জয়নালের ঘুমের মাঝে আবার সেই অদ্ভুত লোকটা এসেছেন।
বজ্রগম্ভীর গলায় বলছেন, এবারে চাচাকেও হারালি, এখনও কি আমার কথায় রাজি হবি না?
জয়নাল বলল, আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?
আমার কথা না শুনলে একে-একে সবাইকে হারাবি। এরপর পর্যায়ক্রমে তোর দুই চাচাতো ভাই। প্রয়োজনে সমস্ত গ্রাম উজাড় করে ফেলব।
জয়নাল বিস্মিত গলায় বলল, আপনার কথার মানে। বুঝতে পারছি না।
তুই কী ভেবেছিস, তোর বাবার আর চাচার মৃত্যু এমনিতেই হয়েছে? তোর কারণে হয়েছে। তুই আমার কথায় রাজি হসনি বলে তাঁদের মরতে হলো।
জয়নাল অবাক গলায় বলল, আমার কারণে তাদের মৃত্যু হবে কেন?! বাবা মারা গেছেন ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে, চাচা মারা গেছেন সাপের ছোবলে।
পঞ্চবক্র হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, আমার হাতে যে আঁকা-বাঁকা লাঠিটা দেখিস, এটা কোনও সাধারণ লাঠি নয়। এটা সাক্ষাৎ মৃত্যু। এই লাঠি আমি যার নাম বলে ছুঁড়ে মারব তার মৃত্যু ঘটবে। লাঠি মাটিতে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে জীবন্ত হয়ে উঠবে। যাকে মারতে যে রূপের প্রয়োজন সেই রূপ নেবে। তোর বাবাকে মারতে চিলের রূপ, আর চাচাকে মারতে সাপের রূপ নিয়েছিল। তুই যদি আরও মৃত্যু দেখতে চাস কী আর করার! তোকে আমার চাই-ই চাই।
জয়নাল বুঝতে পারল তান্ত্রিক পঞ্চবক্র যা বলছেন ঠিকই বলছেন। তার অনেক ক্ষমতা। তিনি চাইলে সব কিছুই করতে পারেন। সে মরিয়া গলায় বলে উঠল, তারচেয়ে আপনি আমাকেই মেরে ফেলেন।
না, তোকে কিছুতেই মারা যাবে না। তোকে পাবার জন্য পৃথিবীর সবাইকে মেরে ফেললেও, তোকে কিছুতেই মারব না। না অন্য কাউকে তোক মারতে দেব।
আপনি কী চান আমার কাছে?
কতবার বলেছি আমি শুধু তোকে চাই। তোকে নিয়ে যেতে চাই। ইচ্ছে করলে আমি তোকে সম্মোহন করেও নিতে পারতাম। কিন্তু তাতে আমার কাজ হবে না। তোকে নিজের ইচ্ছেতে যেতে হবে। যতক্ষণ না তুই রাজি হবি, তোকে বাধ্য করার জন্য সব করব আমি।
জয়নাল হার মানা গলায় বলল, ঠিক আছে, আমি আপনার সঙ্গে যাব।
তান্ত্রিকের চেহারায় পরিতৃপ্তির ছাপ দেখা গেল। চোখ দুটো আনন্দে ঝলমল করে উঠল। আয়েশি গলায় বললেন, চল, তা হলে।
.
জয়নাল তান্ত্রিক পঞ্চবক্রের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। নিশুতি রাত। আকাশে ঘোলাটে চাঁদ। চারদিক থমথম করছে। কোথাও কেউ নেই। গভীর ঘুমে তলিয়ে আছে সমস্ত গ্রাম। এমনকী আশপাশে কোনও রাত জাগা কুকুর-বিড়ালও দেখা যাচ্ছে না। যেন কোনও অশুভ শক্তির ভয়ে সবাই লুকিয়ে রয়েছে।
জয়নাল তান্ত্রিকের পিছু-পিছু এগিয়ে যাচ্ছে। কী আশ্চর্য! চাঁদের আলোতে জয়নালের ছায়া পড়ছে, কিন্তু তান্ত্রিকের ছায়া দেখা যাচ্ছে না।
তান্ত্রিক জয়নালকে নিয়ে গ্রামের উত্তর দিকের শেষ মাথায় ঘন জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। এই জঙ্গল সুন্দরবনের একটা অংশ। এখান থেকে যতই সামনে এগোবে ততই সুন্দরবনের গভীরে চলে যাবে।
তান্ত্রিক জয়নালকে নিয়ে জঙ্গল চিরে এগিয়েই যাচ্ছেন। কোথায় তার গন্তব্য কে জানে! পথ যেন আর ফুরোবার নয়! ক্লান্তিতে জয়নালের শরীর ভেঙে আসছে। বার-বার হাই উঠছে। যেন চলতে-চলতেই সে ঘুমিয়ে পড়বে।
রাত ফুরিয়ে চারদিক ফর্সা হয়ে উঠছে। পাখির কলতানে নতুন একটা দিনের সূচনা হচ্ছে। তান্ত্রিক আর জয়নাল গিয়ে পৌঁছেছে জঙ্গলের মাঝের পরিত্যক্ত এক শ্মশান কালী মন্দিরে। বিশাল জায়গা জুড়ে পলেস্তারা খসে পড়া, শেওলা ধরা, রাজ্যের আগাছা গায়ে জড়িয়ে কোনওক্রমে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভাঙাচোরা কাঠামোটা। কমপক্ষে দেড়-দুশো বছর আগে হয়তো শ্মশানের পাশ ঘেঁষে কেউ এই মন্দির নির্মাণ করেছিল। এখন অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে গত একশো বছরেও কেউ হয়তো এই মন্দিরের চাতালে পা রাখেনি। শ্মশানেও হয়নি কোনও শবদেহ পোড়ানো।
তান্ত্রিক জয়নালকে মন্দিরের ভিতরে এক গুপ্ত কামরায় নিয়ে গেলেন। এটাই বোধহয় তান্ত্রিকের ডেরা। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।
তান্ত্রিক বললেন, আমার সঙ্গে এখানেই থাকবি তুই।
জয়নাল কিছু বলল না। পথশ্রমে তার শরীর ভেঙে আসছে।
তান্ত্রিক বললেন, যা, নদী থেকে স্নান করে আয়। মন্দিরের পাশ ঘেঁষেই একটা নদী বয়ে গেছে। পঞ্চাশ-ষাট হাত এগোলেই নদীটা দেখতে পাবি। ততক্ষণে আমি তোর খাওয়ার ব্যবস্থা করছি।
জয়নাল নদী থেকে গোসল করে এল। তান্ত্রিক তার খাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। আস্ত দুটো ঝলসানো বন মোরগ, পোড়া বুনো আলু, আর নানান ধরনের বুনো ফল-মূল।
জয়নাল দেরি না করে খেতে বসল। সারা রাত ধরে হেঁটে আসায় পেটে তার কুমিরের খিদে। খাবার দেখে নিজেকে। আর সামলাতে পারল না।
জয়নাল গোগ্রাসে খাচ্ছে আর তান্ত্রিক দূরে বসে তৃপ্তি ভরা চোখে তার খাওয়া দেখছেন। খেতে-খেতে জয়নালের খেয়াল হলো তান্ত্রিক নিজে কিছুই খাচ্ছেন না। সে বুনো মোরগের রান চিবুতে-চিবুতে বলে উঠল, আপনি কিছু খাচ্ছেন না। কেন?
তান্ত্রিক বললেন, আমার খাওয়ার দরকার হয় না। মানুষ খায় কেন? শরীরে শক্তি জোগানোর জন্য। আমি ধ্যানে বসে সরাসরি সূর্যের আলো আর বাতাস থেকে শক্তি শুষে নিই।
জয়নালের খাওয়া শেষ হলে তান্ত্রিক বললেন, আমি এখন ধ্যানে বসছি। ধ্যানমগ্ন অবস্থায় আমাকে কখনও বিরক্ত করবি না।
জয়নাল কিছু না বলে ওপাশে মাদুরের উপর গিয়ে শুয়ে পড়ল। খুব ঘুম পাচ্ছে তার। চোখ দুটো আর মেলে রাখতে পারছে না।
পাঁচ
তান্ত্রিকের আস্তানায় জয়নালের প্রায় সপ্তাহ দুই কেটে গেছে। প্রতি বেলায়ই তান্ত্রিক তাকে যথা সম্ভব ভাল-ভাল খাবার দাবার দিচ্ছেন। ঝলসানো বন মোরগ, না হয় ঝলসানো হরিণের মাংস, পাখির মাংস, বুনো হাঁসের মাংস, বুনো মহিষের মাংস, কবুতরের মাংস, নদী থেকে ধরে আনা বড় বড় মাছ-কিছু একটা থাকছেই। সেই সঙ্গে সিদ্ধ বুনো আলু, সিদ্ধ কচি বাঁশের কাণ্ড, সিদ্ধ সবজি, মধু, বুনো কলা, আম, লিচু, কাঁঠাল, ডালিম সহ নাম না জানা অনেক বুনো ফল মূল।
তান্ত্রিক এসব খাবার কীভাবে সংগ্রহ করেন সেটা জয়নাল বুঝতে পারছে না। সব সময়ই ধ্যানে মগ্ন থাকেন, অথচ খাওয়ার বেলায় ঠিকই জয়নালের সামনে এসব খাবার পরিবেশন করছেন। অবশ্য এই জঙ্গলে এ সবই পাওয়া যায়।
তান্ত্রিকের আস্তানায় জয়নালের দিনগুলো খুব একটা খারাপ কাটছে না। বলা যায় জামাই আদর পাচ্ছে। কিন্তু তাকে কী জন্য আনা হয়েছে সেটা তান্ত্রিক এখনও বলেননি। জয়নালের মনে ভয় জাগছে, তান্ত্রিকের আস্তানাটা হচ্ছে শত বছরের পুরানো একটা শোন কালী মন্দির, শুনেছে মা কালীর সামনে অনেক সময় নরবলি দেয়া হয়-তান্ত্রিক কি তা হলে তাকে বলি দেবার উদ্দেশ্যে এনেছেন? বলি দেবার আগে খাইয়ে-পরিয়ে হৃষ্ট-পুষ্ট করে নিচ্ছেন? তবে এই মন্দিরের মূর্তির বেদির জায়গাটা খালি। সেখানে কোনও কালী মূর্তি নেই। কোনও এক সময় হয়তো ছিল। কেউ সেটাকে সরিয়ে ফেলেছে বা চুরি করে নিয়ে গেছে।
জয়নাল রাতের খাওয়া শেষ করে উঠল। একট দরেই তান্ত্রিক পদ্মাসনে বসে আছেন। জয়নাল ভীত গলায় জিজ্ঞেস করল, আপনার এখানে অনেক দিন হয়ে গেল, কিন্তু এখনও জানতে পারলাম না কেন আমাকে নিয়ে এসেছেন!
তান্ত্রিক আয়েশি গলায় বললেন, সময় হলেই জানতে পারবি। সময় প্রায় হয়ে এসেছে। আর বেশি দেরি নেই।
জয়নাল বলে উঠল, আপনি কি আমাকে বলি দেবেন?
তান্ত্রিক ধমকে উঠলেন, আহাম্মকের মত কথা বলবি না। আমি তোকে বলি দেব কেন? আগেই বলেছি না তোকে পাওয়ার জন্য পৃথিবীর সবাইকে মেরে ফেলতে পারি, কিন্তু তোকে কিছুতেই মরতে দেব না।
তা হলে কেন আমাকে নিয়ে এসেছেন? বলিও দেবেন না, আপনার কী কাজে আমি লাগতে পারি?
আমার মেয়েকে তোর কাছে বিয়ে দেব।
জয়নাল হতবাক হয়ে গেল। মেয়েকে তার কাছে বিয়ে দেবার জন্য তার বাবা-চাচাকে মেরে তান্ত্রিক তাকে এভাবে নিয়ে এসেছেন!
জয়নাল বসে-যাওয়া গলায় প্রশ্ন করল, আপনার মেয়ে আছে?
তান্ত্রিক কিছুটা বিষাদগ্রস্ত গলায় বললেন, হ্যাঁ, আমার একটি মেয়ে আছে। পরীর চেয়েও রূপবতী মেয়ে।
জয়নাল বলল, পৃথিবীতে কি ছেলের অভাব আছে? আপনার মেয়েকে বিয়ে দেবার জন্য আমাকেই বেছে নিতে হলো?
তান্ত্রিক বললেন, তুই ছাড়া পৃথিবীর আর কেউই আমার মেয়ের যোগ্য নয়।
কী এমন আছে আমার মাঝে, যে আমার কাছেই আপনার মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে?
আমার মেয়েকে বিয়ে দেবার জন্য এমন একটা ছেলের প্রয়োজন ছিল যার জন্ম শুক্লপক্ষের তেরোতম রাত্রির পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের মুহূর্তে। যে জন্মের পরপরই মাকে হারিয়েছে। বড় হয়েছে কোনও নারীর আদর-ভালবাসা আর স্পর্শ ছাড়া। বড় হয়েও কোনও নারীর সান্নিধ্য পায়নি। প্রেম-ভালবাসার সম্পর্কেও জড়ায়নি। হারায়নি কুমারত্ব। অথবা কোনও নারীকে নষ্ট করেনি বা হত্যা করেনি। কোনও মাদী জন্তু জানোয়ারও হত্যা করেনি। একজন নারীকে নষ্ট করা আর হত্যা করা একই ব্যাপার। মোদ্দা কথা, এমন একজন যার দ্বারা কোনও দিনও কোনও নারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। অথচ সে কোনও দিন কোনও নারীর ভালবাসা পায়নি। এই সব বৈশিষ্ট্যই রয়েছে তোর মাঝে। তোর জন্ম শুক্লপক্ষের। তেরোতম রাত্রিতে পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের মুহূর্তে। জন্মের পরই মা মারা গেছে। বড় হয়েছিস বাবার কোলে। মায়ের অবর্তমানে খালা, ফুপু, মামী, চাচী, নানী, দাদী বা বড় বোন সম্পর্কিত কারও কোলেই বড় হসনি। মুখচোরা লাজুক স্বভাবের বলে বড় হয়েও কোনও নারীর কাছে যাসনি। কোনও মাদী জন্তু জানোয়ারও হত্যা করিসনি। হত্যা করা তো দূরের কথা, কোনও জন্তুকে তোর সামনে অন্য কেউ হত্যা করতে গেলেও ভয়ে পালিয়ে যাস। তা মাদী বা মর্দা যে, কোনও ধরনের জন্তুই হোক।
জয়নাল ভেবে দেখল তান্ত্রিক তার সম্পর্কে যা বলছেন সব ঠিকই বলছেন। তার সামনে কেউ মুরগি-হাঁস জবাই করতে নিলেও সে ভয়ে কুঁকড়ে যায়। তাই তার বাবা বাড়িতে কখনও মুরগি-হাঁস জবাই দিতেন না। ছোটবেলা থেকেই তার এই মানসিক সমস্যাটা রয়েছে।
জয়নাল বলল, এসব বৈশিষ্ট্যের কারণে আপনি আপনার মেয়েকে আমার কাছে বিয়ে দিতে চান, এ কথাটা তো সহজভাবেও বলা যেত। আমার বাবা-চাচাকে হত্যা করে আমাকে বাধ্য না করলেও পারতেন।
সহজভাবে বললে তুই রাজি হতি না।
কেন রাজি হতাম না? আপনার মেয়ে নাকি অসম্ভব রূপবতী!
তান্ত্রিক একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, আমার মেয়ে জীবিত নয়, মৃত। মৃত মেয়েকে বিয়ে করতে কেউ কি রাজি হয়?
কথাটা শুনে জয়নালের মুখ হাঁ হয়ে গেল। বিস্ময়ে চোখ কপালে উঠল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে অস্ফুটে বলল, আপনার মেয়ে মত?!
তান্ত্রিক বলতে লাগলেন, হ্যাঁ, মৃত। প্রায় দেড়শো বছর আগে মারা গেছে আমার এই মেয়ে। আমি তখন কালী মন্দিরের সাধারণ এক পুরোহিত ছিলাম। মা মরা মেয়ে আমার। তিন দিনের জ্বরে মেয়েটা আমার কুমারী অবস্থায় মারা যায়। মেয়ের মৃত্যুতে মাথা খারাপের মত অবস্থা হয় আমার। প্রাচীন লিপি, পুঁথি এসব নিয়ে আমার অনেক পড়াশোনা ছিল। প্রাচীন এক পুঁথিতে পেয়েছিলাম এক মস্ত অপদেবতা রয়েছেন, যার আরাধনা করে মৃত্যুকে রোখা যায়, মৃত মানুষকে আবার জীবিত করা যায়।
আমি লোকালয় থেকে পালিয়ে জঙ্গলের পরিত্যক্ত এই মন্দিরে এসে সেই অপদেবতার আরাধনা শুরু করি। প্রথমে অপদেবতা আমাকে নিজের মৃত্যুকে পরাজিত করার ক্ষমতা দেন। এরপর ক্ষমতা আসে অন্যকে মৃত্যু শাস্তি দেবার, আমার হাতের এই আঁকা-বাঁকা লাঠির মাধ্যমে। আরও একশো বছর ধরে আরাধনা চালিয়ে যাবার পর মেয়েকে বাঁচিয়ে তোলার ক্ষমতাও আসে। কিন্তু সে ক্ষেত্রে তোর মত নিষ্পাপ এক যুবকের প্রয়োজন পড়ে। যার দ্বারা কোনও দিনও কোনও নারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। তেমন এক যুবকের সান্নিধ্যেই পুনর্জীবন লাভ করবে আমার মেয়ে। আবার গড়ে উঠবে তার দেহ। আমার কাঁধে সব সময় এই যে কাপড়ের পুঁটলিটা দেখিস, এটার মধ্যেই রয়েছে আমার মেয়ের অস্থি। এই অস্থির সঙ্গেই তোর বিয়ে হবে। তোর জন্ম তিথিতে। শুক্লপক্ষের তেরোতম রাত্রির পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণের মুহূর্তে। খুব শীঘ্রিই আসছে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। আর মাত্র দুই সপ্তাহ বাকি।
ছয়
শুক্লপক্ষের তেরোতম রাত। রাত একটা এক মিনিট থেকে পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ শুরু হবে। শেষ হবে একটা তেত্রিশ মিনিটে। চন্দ্রগ্রহণের এই মুহূর্তে তান্ত্রিকের মেয়ের কঙ্কালের সঙ্গে জয়নালের বিয়ে সম্পন্ন হবে। বিয়ে হবার পরপরই পুনর্জীবন লাভ করবে তান্ত্রিকের মেয়ে। বিয়ের সব আয়োজন শেষ। অপেক্ষা শুধু চন্দ্রগ্রহণের।
জয়নাল নদী থেকে স্নান করে এসেছে। নগ্ন হয়ে পর-পর তিনটা ডুব দিয়ে সেলাইবিহীন এক খণ্ড সাদা কাপড় কোমরে জড়িয়ে, একবারের জন্যও পিছনে না তাকিয়ে সোজা মন্দিরের চাতালে এসে পৌঁছেছে। আসার পথে বার-বারই মনে হয়েছে ভয়ঙ্কর কিছু একটা তার পিছু-পিছু চলে আসছে। কিন্তু তান্ত্রিকের নির্দেশ মেনে একবারের জন্যও পিছনে তাকায়নি।
মন্দিরের চাতালের ঠিক মাঝ বরাবর দাউদাউ করে জ্বলছে আগুন। আগুনকে সামনে রেখে পদ্মাসনে বসেছেন তান্ত্রিক। আগুনের সামনে লাল সালু কাপড়ের উপর মানুষের আকৃতিতে লম্বালম্বিভাবে বিছিয়ে রাখা হয়েছে তান্ত্রিকের মেয়ের কঙ্কাল। মাথার জায়গায় খুলি, এরপর গলার হাড়, পাঁজরের হাড়, উরুর হাড়, পায়ের জায়গায় পায়ের হাড়-যথাক্রমে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। লাল রঙের এক বিয়ের শাড়ি দিয়ে উপর থেকে ঢেকে দেয়া হয়েছে লাল সালুতে বিছিয়ে রাখা হাড়-গোড়গুলোকে। শুধু খুলিটা বাইরে বেরিয়ে আছে।
তান্ত্রিক উচ্চস্বরে দুর্বোধ্য বিভিন্ন মন্ত্র-তন্ত্র আওড়ে যাচ্ছেন আর সামনে থাকা আগুন একটু পর-পর উসকে দিচ্ছেন। চন্দন কাঠের টুকরো আগুনে ঠেলে দিচ্ছেন, ঘি ঢালছেন, ঢালছেন করমচা তেল, ছিটাচ্ছেন ধূপ-ধুনো আর লোবানের গুঁড়ো সহ আরও যেন কী সব। ওদিকে আগুনের সামনে থাকা কঙ্কালের উপর ছিটিয়ে দিচ্ছেন মন্ত্রপূত জল, আতর-গোলাপজল সহ বিভিন্ন সুগন্ধী।
চন্দ্রগ্রহণ শুরু হবার ঠিক আগমুহূর্তে তান্ত্রিক জয়নালকে নির্দেশ দিলেন কঙ্কালের উপর গিয়ে বসতে। শবসাধনার ভঙ্গিতে কঙ্কালের পেট বরাবর উঠে বসতে হবে।
জয়নাল তা-ই করল। কঙ্কালের পেট বরাবর উঠে বসল। তান্ত্রিক মন্ত্র-তন্ত্র চালিয়েই যাচ্ছেন। ওদিকে মাথার উপর আকাশে চাঁদটা ধীরে-ধীরে সম্পূর্ণ গ্রাস হয়ে যাচ্ছে। নেমে আসছে অন্ধকার।
চাঁদ পুরোপুরি গ্রাস হবার পর তান্ত্রিক ওকে নির্দেশ দিলেন কঙ্কালের খুলিতে সিঁদুর মাখিয়ে দিয়ে নেমে আসতে।
জয়নাল কঙ্কালের খুলিতে সিঁদুর মাখিয়ে নেমে এল। চাঁদটাও গ্রাসমুক্ত হতে শুরু করল। আলোর রেখার মত চাঁদের সামান্য অংশ দেখা গেল। সেই রেখা ক্রমেই বিস্তার লাভ করতে থাকল।
গ্রাসমুক্ত হতে থাকা চাঁদের আলো বনভূমিতে এসে পৌঁছতেই প্রচণ্ড দমকা হাওয়া ছাড়ল। চাঁদের গ্রাসমুক্ত হওয়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দমকা হাওয়া ধীরে-ধীরে ঝড়ো হাওয়ায় রূপ নিল। হাওয়ার তোড়ে তান্ত্রিকের সামনের আগুন নিভে। গেল। কঙ্কালটিকে ঢেকে রাখা বিয়ের শাড়িটাও উড়ে গেল।
কী আশ্চর্য! কঙ্কালের পাঁজরের মাঝে একটা হৃৎপিণ্ড দেখা যাচ্ছে! জীবন্ত! ধক-ধক করে হৃৎপিণ্ডটা লাফাচ্ছে।
ঝড়ের তীব্রতা আরও বেড়েছে। ঝড়ো হাওয়া আশপাশের সব ধুলো-বালি উড়িয়ে আনছে। ওগুলো উড়ে এসে কঙ্কালের গায়ে লেপ্টে যাচ্ছে।
লেপ্টে যাওয়া ধুলো-বালিগুলো ধীরে-ধীরে কঙ্কালের গায়ে রক্ত-মাংস, শিরা-উপশিরা আর চামড়ার রূপ নিচ্ছে। পা থেকে শুরু হয়েছে। প্রথমে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল। এরপর সবগুলো আঙুল। পায়ের পাতা। এক সময় সম্পূর্ণ পা। পর্যায়ক্রমে পা থেকে উপরের দিকে সবগুলো অঙ্গ গড়ে উঠতে লাগল। নমনীয়-কমনীয় মাখনের মত ফর্সা মোলায়েম নারী অঙ্গ।
তান্ত্রিক অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। হাসতে-হাসতে চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, পেরেছি! আমি পেরেছি! আমার সাধনা সফল হয়েছে! আমার মেয়েকে আবার জীবিত করতে। পেরেছি…
সব ঠিকঠাকই হচ্ছিল। কঙ্কালের কাঁধ পর্যন্ত নারীর অঙ্গ সৌষ্ঠবই গড়ে উঠেছে। কাঁধের উপরে গলা থেকে দেখা দিল বিকৃতি। নারীর মুখের জায়গায় গড়ে উঠেছে শিয়ালের মুখ।
তান্ত্রিকের হাসি থেমে গেল। মুহূর্তে তার চেহারায় নেমে এল এক রাশ আতঙ্ক। আতঙ্কিত তান্ত্রিক আর্তচিৎকারের মত করে বলে উঠলেন, একী হচ্ছে?! এমন তো হওয়ার কথা ছিল না! কোথায় ভুল করেছি? আমার মেয়ের মুখের জায়গায়
কেন শিয়ালের মুখ গড়ে উঠেছে?
এবারে হেসে উঠল জয়নাল। হাসতে-হাসতে বলতে লাগল, তান্ত্রিক পঞ্চবক্র, তুই ভেবেছিস কী, আমার বাবা চাচাকে মেরে আমাকে বাধ্য করে তোর মেয়েকে তুই ফেরত পাবি? আমি কোনও প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করব না? শুধু মুখ বুজে সব সহ্য করে যাব? তোর মুখ থেকে শুনে এবং তোর অবর্তমানে তোর ডেরায় থাকা পুরানো পুথি পড়ে এটা বুঝতে পেরেছিলাম আমি যদি কোনও নারীর প্রতি অন্যায় করি, বা নিজের কুমারত্ব নষ্ট করি, তা হলে তুই সফল হতে পারবি না। সেই চেষ্টাই নিই। তুই যখন ধ্যানে থাকিস তখন এই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে কোনও প্রতিতালয়ে গিয়ে নিজের কুমারত্ব নষ্ট করে আসতে চাই। সেই চেষ্টা আমার সফল হয় না। দিনের পর দিন জঙ্গলে ঘুরে মরি কিন্তু জঙ্গল থেকে কিছুতেই বেরোতে পারি না। পথ গুলিয়ে ফেলি। তুই হয়তো নজরবন্দি করে রেখেছিলি। বার-বার ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসি। হাতে আর সময় থাকে না। আজকের এই রাত এসে যায়। তোকে বিফল করতে কিছুই আর করার থাকে না। আমাকে নদী থেকে, পর-পর তিনটা ডুব দিয়ে স্নান করে আসতে বলিস। নদীতে যাওয়ার পথে হঠাৎ মাথায় খেয়াল আসে। জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর সময় দুটো বাচ্চা সহ একটি মা শিয়ালকে দেখেছিলাম। শিয়ালটার বাসাও দেখেছিলাম। মোটা একটা গাছের খোড়লে। বাচ্চা দুটো বড় হয়ে গেছে। মায়ের অভাবে এখন আর মারা পড়বে না। আমি গিয়ে গাছের খোড়লের ভিতর থেকে শিয়ালটাকে বের করে হত্যা করি। জীবনে প্রথম কোনও জন্তুকে হত্যা। তা-ও আবার একটা মাদী জন্তু। শিয়ালটার রক্ত সারা গায়ে মেখে নদী থেকে গোসল করে আসি। তুই কিছুই বুঝতে পারিসনি। তুই হয়তো মেয়েকে বাঁচিয়ে ভোলার যজ্ঞ নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিলি যে কিছুই ধরতে পারিসনি।
চাঁদটা পুরোপুরি গ্রাসমুক্ত হয়েছে। ঝড় থেমে গেছে। চারদিক থমথম করছে। সেই সঙ্গে তান্ত্রিকের মুখটাও।
তান্ত্রিকের মেয়ে বেঁচে উঠেছে। রূপবতী কোনও নারী নয়, অদ্ভুত এক জম্ভ হয়ে। পুরো শরীর মেয়েমানুষের মত, শুধু মাথাটা শিয়ালের।
অদ্ভুত জন্তুটা গা ঝাড়া দিয়ে চার হাত-পায়ে উঠে দাঁড়াল। ক্রোধের হুঙ্কার ছাড়তে লাগল। মুখ থেকে গড়িয়ে নামছে লালা। মুখের দুপাশ থেকে বেরিয়ে পড়েছে লম্বা শ্বদন্ত। হাতে-পায়েও গজিয়ে উঠেছে হিংস্র জন্তুর মত লম্বা সূচালো তীক্ষ্ণ নখ।
তান্ত্রিক আহত গলায় চিৎকার করে উঠলেন, কাজটা তুই ঠিক করলি না। মোটেই ঠিক করলি না। তন্ত্রবিদ্যার কিছুই না জেনে ভুল পদক্ষেপে প্রতিশোধ নিতে গিয়ে তুই ভয়ঙ্কর এক। পিশাচীকে ডেকে এনেছিস। যে পিশাচী নারী এবং শিয়ালীর অস্তিত্বে ভর করে নরক থেকে চলে এসেছে। তুই শুধু তোের আর আমারই বিপদ ডেকে আনিসনি, পুরো মানব জাতির জন্যও বিপদ ডেকে এনেছিস।
তান্ত্রিকের বলা শেষ হবার আগেই শিয়াল এবং নারীর মিশেল, অদ্ভুত দেখতে জন্তুটা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লম্বা-লম্বা সূচালো নখযুক্ত একটা হাত তার পেটের ভিতর ঢুকিয়ে দিল। রক্তে ভেসে যেতে লাগল তান্ত্রিকের পুরো শরীর। হাতটা টেনে বের করে নিল কলিজাটা। এরপর রক্ত মাখা কলিজাটা কচ-কচ করে চিবিয়ে খেতে আরম্ভ করল।
মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে-করতে তান্ত্রিকের দেহ নিথর হয়ে গেল। ততক্ষণে অদ্ভুত জন্তুটা তান্ত্রিকের কলিজাটাও খেয়ে শেষ করেছে। এবারে ওটা চোখ তুলে তাকাল জয়নালের দিকে।
জয়নাল বুঝতে পারল ওটার লক্ষ্য এখন সে। এক মুহূর্তও আর দেরি না করে সে পড়িমরি করে ছুটতে শুরু করল। জন্তুটাও থেমে রইল না। ধাওয়া শুরু করল। চার হাত-পায়ে চিতা বাঘের গতি ওটার।
ফুটফুটে চাঁদের আলোতে দিগ্বিদিজ্ঞানশূন্য জয়নাল ছুটতে-ছুটতে নদীর পাড়ে এসে পড়ল। কীসের সঙ্গে যেন পা হড়কে চাঁদের আলোতে ঝিকমিক করা নদীতটের বালির উপর আছড়ে পড়ল। সেই সুযোগে ধাওয়া করে আসা অদ্ভুত জন্তুটা তার উপর চেপে বসল।
কী অবাক কাণ্ড! জন্তুটা তাকে মারছে না! বরং আদর। জানাচ্ছে! পশুরা যেভাবে আদরের ভাষা জানায়। নাক দিয়ে তার গায়ের গন্ধ শুঁকছে। জিভ দিয়ে শরীর চেটে দিচ্ছে। গায়ের সঙ্গে গা ঘষছে। চার হাত-পায়ে জড়িয়ে ধরে লুটোপুটি খেলার চেষ্টা করছে।
হঠাৎ সুযোগ এসে গেল জয়নালের। লুটোপুটি খেলতে গিয়ে জন্তুটার চার হাত-পায়ের বাধন আলগা হয়ে গেছে। সেই সুযোগে জয়নাল লাফ দিয়ে সরে গিয়ে হাঁচড়ে-পাঁচড়ে নদীতে নেমে পড়ল। জটা তাকে আর ধরার চেষ্টা না করে নদীতটে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকল।
সাঁতার কেটে বেশি দূর এগোতে পারল না জয়নাল। ভয়ে-আতঙ্কে টেনে-টেনে শ্বাস নিতে থাকায় নাকের ফুটো দিয়ে শ্বাসনালীতে পানি ঢুকে পড়ছে। ভয়ানক কাশি উঠল। কাশির দমকে শ্বাস টেনে আর কুলোতে পারল না। জ্ঞান। হারিয়ে নদীর গভীরে তলিয়ে গেল।
পরিশিষ্ট
জেলেরা নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে নদীর কিনারে চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়সের এক যুবককে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। তারা তাকে উদ্ধার করে জেলে পল্লীতে নিয়ে যায়। তিন দিনেও জ্ঞান ফেরে না যুবকের। তিন দিন পর। যুবক জ্ঞান ফিরে পেলেও তার স্মৃতিশক্তি লোপ পায়। সে তার নাম-ধাম, পরিচয়, বাড়ির ঠিকানা কিছুই বলতে পারে না। শুধু এটুকুই বলে, অদ্ভুত একটা জন্তু তাকে তাড়া করেছিল। জন্তুটার মুখটা শিয়ালের মত আর গলার নিচ থেকে মেয়েমানুষের মত। আর কিছুই মনে নেই তার। ঘুমের মাঝেও যুবক স্বপ্নে সেই অদ্ভুত জন্তুটাকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে। স্বপ্নে জন্তুটা তাকে নিতে আসে। অবশ্য সে দাবি করে সত্যি সত্যিই জন্তুটা তাকে নিতে আসে। জন্তুটা তাকে আদর ভালবাসা জানায়। যেন তার সঙ্গে কোনও এক গোপন সম্পর্ক রয়েছে জটার।
.
কিছুদিন ধরে সুন্দরবনের আশপাশের গ্রামবাসীরা ভয়ানক আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে। তাদের গবাদি পশু, পোষা পাখি সহ বিভিন্ন বয়সী মানুষদেরকে কীসে যেন ধরে নিয়ে যায়। পরে তাদের মৃতদেহ পাওয়া যায়। মৃতদেহের পেটটা চেরা থাকে। পেট চিরে কলিজাটা বের করে নেয়া হয়েছে। কেউ বলছে এটা মানুষখেকো কোনও বাঘ বা চিতা বাঘের কাজ। কেউ বলছে মস্তিষ্ক বিকৃত কোনও মানুষের কাজও হতে পারে। কেউ-কেউ আবার দাবি করছে তারা স্বচক্ষে জানোয়ারটাকে দেখেছে। বাঘ বা চিতা বাঘ কিছুই নয়, শিয়াল জাতীয় অদ্ভুত এক জন্তু। ওটার মুখ শিয়ালের মত, আর শরীরের বাকি অংশ মেয়েমানুষের মত। কেউ আবার দাবি করছে ওরকম জল্প একটা নয়, দুটো। এক জোড়া। একটা পুরুষ, অন্যটা মহিলা। মাঝে-মাঝে পুরুষটাকেও দেখা যায়।
গোরস্থানের কাছে – নাশমান শরীফ
এক
ইনায়া সবসময় নানুর সাথেই থাকে। জন্মের পর থেকে নানুই ওর সব, সেটা বুঝে গেছে। বাবা ব্যস্ত তার ব্যবসা নিয়ে, মা কোর্ট আর ক্লায়েন্ট। নানুও ব্যস্ত তার সংসার নিয়ে।
ইনায়া এটুকু জানে, নানুর সংসারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও। স্বাভাবিকভাবেই নানুর প্রভাব ওর চরিত্রে অনেকখানি। শান্ত-স্নিগ্ধ নরম পরিপাটি ও, দেখতেও নানুর মতই সুশ্রী।
ওরা থাকে উত্তরায়। নানুর বাড়ি মূল শহর থেকে একটু ভেতরে। তবু প্রতিদিনই নানুকে দায়িত্ব পালন করতে হয় ওর। সেটা কখনও হয়তো নানুকে গিয়ে অথবা ওকে নানুর বাসায় নিয়ে।
চতুর্থ শ্রেণীতে পড়লেও বুদ্ধিতে ভীষণ পাকা ও।
অন্যান্য শিশুদের মত গল্প শুনতে ভালবাসে। ভূতের গল্প। পছন্দ করে ও, তবে একটু বড়দের। নানুর গল্প বলতে হয়। ওকে প্রতিদিন।
ইনায়ার মা তানতা গেছে একটা কনফারেন্স-এ যোগ দিতে সিঙ্গাপুর। আর ও এসেছে গ্রামে। এই প্রথম, নানা নানুর সাথে বেড়াতে।
নানু, তোমাদের গ্রামটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে। দেখতে গ্রাম হলেও এখানে তো ঢাকার মত সবই আছে। শুধু এসিটা লাগালেই ঢাকা হয়ে যেত। দুপুরে খাওয়া সেরে নানুর কোলের ভেতর শুয়ে বলছিল ইনায়া।
সেটা ঠিকই বলেছ, নানু, এখন আর এই নাদুরিয়া গ্রাম নেই, যেন এক টুকরো শহর। অথচ জানো, তোমার নানুর ছোটবেলা কেটেছে এই বাড়িতেই, কত ভয়ে! টিমটিমে হারিকেনের আলোয় ভূতের ভয়ে কেঁপেছি।
নানু, তুমি কি সত্যি ভূত কখনও দেখেছ?
হ্যাঁ, দেখেছি। শুধু দেখাই না, ভূত আমার অতি আপনজন।
তা হলে তো আজ তোমার আপন ভূত-এর গল্পই শুনব। বলবে না আমাকে?
না, নানু, তুমি যে ভয় পেতে পারো। ওটা তো তোমার শোনা সাধারণ ভূতের গল্প নয়, ওটা সত্যি আপন। ভূত–অতি আপন!
প্রমিয, নানু! আমি একটুও ভয় পাব না, আর দিনের বেলা ভয় কীসের?
তবে তো বলতেই হয়। ভয় পেলে কিন্তু আমার দোষ নেই, নানু।
দুই
প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগের কথা। রাজবাড়ি জেলার পাংশা থানা। গড়াই নদীর শাখা নদী-স্থানীয় নাম ছোট নদী। তারই এপারে অপূর্ব সুন্দর সাজানো গ্রাম নাদুরিয়া। হয়তো নদীর পারে বলেই নামটা নদীর সাথে মিলিয়ে নাদুরিয়া। ওপারের গ্রামটা আরও সুন্দর। ওটা সরাইল গ্রাম। তখন গ্রামগুলো ছিল অন্ধকারে ঢাকা এক নিভৃত পল্লী। বিদ্যুৎ ছিল না; রাস্তা, যানবাহন, হাসপাতাল, ডাক্তার কিছু ছিল না। সে সময় আশপাশের গ্রামের মেয়েরা হাইস্কুলে পড়তে যেত গড়াই নদীর পাড়ে পাংশা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে।
ওই স্কুলেরই দশম শ্রেণীর ছাত্রী আফসানা। ও আসত সরাইল গ্রাম থেকে। সেটা ছিল স্কুল থেকে দেড় মাইল মানে প্রায় চার কিলোমিটার দূরে।
গ্রামের আরও সঙ্গীদের সাথে হেঁটে যখন কিশোরী আফসানা স্কুলে পৌঁছত, ওর মুখটা মনে হত, ডালিমের মত ফেটে যাবে।
গোলাপি গায়ের বরন কন্যার, মাথা ভরা কেশ। মৃণাল বাহু। দুই গায়ের রূপসী কন্যা সে। তখনকার দিনে পথে ঘাটে অত রূপসী মেয়ে চোখে পড়ত না। তাই কারও ঘরে রূপসী মেয়ে থাকলে তার খবর ছড়িয়ে যেত গ্রাম থেকে গ্রামে।
আর যদি সে হত উঁচু বংশের মেয়ে, তবে তো কথাই নেই। অমুক বাড়ির মেয়ে গো সে। সাথে যদি হত, গুণবতী, তা হলে তো সোনায় সোহাগা।
রূপবতী, গুণবতী, বড় বাড়ির মেয়ে। মানুষের মুখে মুখে ফিরত আফসানার নাম। ওরা অনেক ভাইবোন। আফসানা সারাদিন গৃহকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকত। ছোেট ভাইবোনদের দেখভাল, মাকে সংসারের কাজে সাহায্য, নিজের লেখাপড়া নিঃশব্দে করে চলত। মা গর্ব করে বলতেন, মাটি কাঁপবে তা আমার বেটি কাঁপবে না। বাবা-মা চিন্তিত হয়ে পড়লেন আফসানাকে নিয়ে। প্রায় দিনই দুটো-একটা বিয়ের প্রস্তাব আসে ওর।
তিন
এই, আফসানা, দেখ, মুলাম দাঁড়িয়ে আছে তোর জন্যি। এখন পিছু নেবে আমাদের, দেখিস! কী যন্ত্রণা! প্রতিদিন ছেমড়া তোর জন্যি ওই বটগাছের তলে দাঁড়ায় থাকে। আমরা এলি ও পিছু নেয়। তোর আব্বাকে বলতি হবি। ওই ছেমড়ার মাসের কদিন যায় বুঝবে। মজি চাচা যে মিজাজি মানুষ, ওর টান দে ছিঁড়ে ফেলবিন। বলে আড়চোখে মুলামকে খেয়াল করল মিনু।
তুই বড় বেশি বকিস রে, মিনু। কোনদিক তাকাবিনে। তুই আব্বার কাছে বলে আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা বন্ধ করতি চাস? মিনমিন করে বলল আফসানা।
সরাইল গ্রামের বিখ্যাত হাজীবাড়ি। হাজী সাহেবের বড় ছেলে মজিদ রহমান। এক সময় বাপের জমিদারি ছিল। কালের গর্ভে তা প্রায় বিলীন হয়ে গেছে। জমিদারি না থাকলেও জমিদারি ঠাট-বাট তারা সযত্নে আঁকড়ে আছে। তাদের বাড়ির মেয়ের দিকে সাধারণ ঘরের কেউ চোখ তুলে তাকালে তার যে খবর হবে এটা নিশ্চিত করে বলা যায়।
ওদিকে নাদুরিয়া গ্রামেরই মেম্বার রওশনআরা। বঙ্গবন্ধুর একনিষ্ঠ ভক্ত। তাঁকে ভালবেসেই তার রাজনীতিতে যুক্ত হওয়া। মনে বিশ্বাস, তার প্রিয় আওয়ামী লীগ সংগঠনের একজন কাণ্ডারী একদিন সে হবেই!
এমন নিবেদিত প্রাণ, জনদরদি রাজনৈতিক কর্মীর ঘর সংসার হওয়া কঠিন। তারও হয়নি। সুসংসার প্রত্যাশী স্বামী, ছেলে আর মাকে ফেলে আরেক গাঁয়ে ঘর পেতেছে। ওদিকে মুলাম মায়ের যক্ষের ধন, আদরের দুলাল, তাই তো মা তার নাম রেখেছে মুলাম।
মা দিন-রাত গ্রামের জনগণ আর তার চেলা-চামচা নিয়ে মিটিং করে বেড়াচ্ছে। স্বামী ঘর ছেড়েছে, একমাত্র ছেলে যে বাউণ্ডুলে হয়ে যাচ্ছে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। ছেলের আবদার রক্ষা আর আহ্লাদ দেয়া ছাড়া শাসন বা দায়িত্বে আগ্রহ নেই রওশনআরার।
চার
নাদুরিয়া গ্রামের মেম্বার রওশনআরা এসেছে আফসানাদের বাড়ি। ওর বাবা-মায়ের সাথে দেখা করতে।
আপনার মেয়েটা আমাকে ভিক্ষে দেন, আপা। আমি ওর জীবন দিয়ে হলিও সুখে রাখার চিষ্টা করব। আমার মুলাম যে। ওর না পালি মরে যাবিনি। অনুনয় আকুতিতে রাজি করানোর চেষ্টা করল রওশনআরা আফসানার বাবা-মাকে।
আফসানার মা সম্ভ্রান্ত ঘরের, শিক্ষিত মেয়ে। যথেষ্ট অনুভূতিশীল। তিনি বুঝলেন, স্বামীহারা একমাত্র ছেলের মা, রওশনআরার মনের ব্যথা। তাই তো হাজীবাড়ির সবার বিরুদ্ধে গিয়ে একক সিদ্ধান্তে বিয়েতে রাজি হয়ে গেলেন।
অবশ্য তিনি মেয়ে আফসানার ব্যাপারটা জানতেন। মুখচোরা। মেয়ে কিছু না বললেও বুঝতেন মুলামের প্রতি তার দুর্বলতা তৈরি হয়েছে। মাত্র চোদ্দ বছরের আফসানার বিয়ে হয়ে গেল মুলামের সাথে।
পাঁচ
নাদুরিয়া গ্রামের শেষ সীমা। বিশাল গোরস্থান। আশপাশের দুই-তিন গাঁয়ের লোক মারা গেলে কবর হয় এখানে। প্রায় প্রতিদিনই নতুন-নতুন কবর তৈরি হচ্ছে। এই গোরস্থানের নিকটতম বাড়িখানা মুলামদের। চারপাশে ধু-ধু মাঠ, মাঝখানে বাড়ি। বাড়ির পশ্চিম দিকে কবরস্থান। এ বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়েই মৃতদেহ নেয়া হয় গোরস্থানে। ছোট্ট আফসানা প্রচণ্ড ভীতু। ওদের বাড়িতে বইয়ের লাইব্রেরি ছিল। ছোটবেলা থেকে ভূতের গল্প পড়েছে অসংখ্য। এমন রাজনৈতিক আর ভুতুড়ে পরিবেশে নিজেকে মানানো ওর জন্য কষ্টের। তবু অসম্ভব ধৈর্যশীল, সহিষ্ণু আফসানা মানিয়ে নেয় সবকিছু।
শাশুড়ি মা ব্যস্ত থাকে তার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে। স্বামী-স্ত্রীর নির্দ্বিধায় স্বচ্ছন্দে চলে দিনমান ভালবাসাবাসি। আফসানা লেখাপড়া, গৃহকর্ম, স্বামী, শাশুড়ি সামলানো সবই করে সুনিপুণভাবে। বৈষয়িক সবকিছু বুঝলেও বোঝেনি তার নিজের শরীর। তিন মাসের গর্ভবতী কিশোরী আফসানা বুঝতেই পারেনি সে মা হতে চলেছে।
সেটা না বুঝলেও শরীর আর মন, পরিবর্তনটা জানান দিয়েছে ভালভাবে। এখন সে আরও ভীতু হয়েছে। কদিন ধরেই ভয়টা ভীষণ বেড়েছে তার। গোরস্থানে যেদিন নতুন কেউ ঢুকছে, সেদিন রাতে আর তার ঘুম হয় না। মুলাম সারারাত পোয়াতি বউকে পাহারা দেয়, যত্ন-আত্তি করে।
ছয়
সেদিন অমাবস্যার রাত। সন্ধ্যা লাগতেই চারদিকে ঘুটঘুঁটে অন্ধকার। মুলাম গেছে উত্তরপাড়া জরুরি কাজে, শাশুড়ি মা গেছে তার মিটিঙে। ঘরে হারিকেন জেলে খাটের ওপর বসে আছে আফসানা। প্রচণ্ড ভয় লাগছে ওর। আজ নতুন একটা কবর হয়েছে। একটু পরেই মুলাম চলে আসবে, সেটুকু সময়ও একা থাকা কঠিন ওর কাছে।
হঠাৎ থপথপ একটা শব্দ! আফসানা সচকিত হলো। শব্দটা হচ্ছে খাটের তলায়। এ ঘরে আবার দুতিনটে কুনোব্যাঙ আছে। যদিও ভয়ে সিঁটিয়ে যাচ্ছে, তবু ও ব্যাঙের কথাই ভাবল।।
ওটা কী? স্পষ্ট ওর সামনে, খাটের তলা থেকে বের হলো মাথাটা! ছোট্ট একটা চিনে পুতুলের মত। ধবধবে সাদা চোখজোড়া বন্ধ। স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে আফসানা। অতিরিক্ত ভয়ে শক্ত হয়ে গেছে ও। হঠাৎ মাথাটা নড়ে উঠল। কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল ও। একটা শিশুর মাথা ওটা। শরীরটা দেখার চেষ্টা করল। না, শরীর নেই বা হয়তো আছে, ও দেখতে পাচ্ছে না। হঠাৎ মাথাটা চোখ খুলল। তার মুখ দিয়ে অস্ফুটে বেরিয়ে এল, মা।
আফসানা চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারাল।
মুলাম বউকে সেবা-যত্ন, সঙ্গ দেয়া বাড়িয়ে দিল অনেকগুণ। দিনরাত সানা মানে আফসানাকে আদর-আহ্লাদ করাই এখন ওর প্রধান কর্ম।
ও, মা, তুই আর সন্ধের পর বাইরে থাকবিনে। আমার সানা ভয় পায় যে, আহ্লাদ করে মাকে বলল মুলাম।
হ্যাঁ, তাই তো তুই তোর কাজকম্ম রেখে দিনরাত পাখির সানা নিয়ে আছিস, আবার এখন আমার কাজকম্মও ছাড়তে কচ্ছিস, একটু জোর গলায় বলল রওশনআরা। যদিও আফসানাকে সে-ও কম ভালবাসে না। নিজে অসংসারী হলেও আদরের বৌমাকে সময় দেয়া বা রেধে খাওয়াতে চেষ্টা করে সে।
মুলাম সারারাত বউকে জড়িয়ে ধরে ঘুমায়। হারিকেন নিভিয়ে দিলে ঘরটা একেবারে ঘুটঘুঁটে অন্ধকার হয়ে যায়। মুলাম মাথার কাছে জানালাটা খুলে দিল। যদিও অন্ধকার রাত তবুও কিছুটা আলো হলো ঘরটা। জানালার পাশে হাস্নাহেনার ঝোঁপটায় অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে। ফুলের গন্ধে ম-ম চারদিক। বুকের মাঝে সানাকে জড়িয়ে আধো ঘুম জাগরণে পাখা দিয়ে বাতাস করছিল মুলাম।
বাতাস আর ফুলের গন্ধে একাকার…আফসানা জানালার ফাঁক গলে আসা হালকা আলো আর বাতাসের অপার্থিব সৌন্দর্য উপভোগ করছিল। মুলাম পাখা হাতে ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ জানালার পাশে থপথপ করে শব্দ…
সচকিত হলো আফসানা। স্বামীর হাতটা ভাল করে টেনে নিল বুকের ওপর। ও স্পষ্ট শুনছে মাথার কাছে কেউ চিউ চিউ করে ডাকছে, ম…ম।
ও ঘোরের ভেতর চলে গেল। যদিও শরীর অসাড় তবু ঘুরে তাকাল জানালায়। সেই মাথা! শুধু মাথাটাই দেখা যাচ্ছে জানালায়।
আস্তে টোকা দিল স্বামীকে। মুলাম ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।
এই, কী হয়েছে? কী হয়েছে তোমার? আবার কিছু দেখেছ?
কাত হয়ে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে আছে জানালার দিকে আফসানা। মুখে কোন শব্দ নেই।
দিনকে দিন শরীরটা অবনতির দিকে যাচ্ছে আফসানার। খাওয়া-দাওয়া করে নামে মাত্র। ঘুমও কম। শুধু পেটটা বাড়ছে অতি দ্রুত।
বাড়ির পাশেই পুকুর। মুলাম গেছে হাটে। পুকুরঘাটে বসে আছে রওশনআরা। গোসল করছে আফসানা। একমাত্র গোসল করতেই ওর আরাম বোধ হয় শরীরে। শীর্ণ দেহ, এক মুহূর্ত মা-ছেলে কেউ চোখের আড়াল করে না বউকে। পাছে কোন দুর্ঘটনা ঘটে।
পানিতে ডুব দিল ও। কিছু একটা ওর শাড়ির আঁচলের তলে নড়ে উঠল। ও আস্তে করে আঁচল টান দিতেই মাথাটা মা বলে ডেকে উঠল।
মা-গো, বলে চেঁচিয়ে পাড়ে উঠে এল আফসানা।
সাত
আফসানা এখন ওর প্রিয় পুকুরে আর গোসল করতে নামে না। গোসলখানাতেই গোসল করে। রাতে যত, দম বন্ধই লাগুক জানালা খোলে না; যত জরুরি কাজই থাকুক, কেউ ওকে একা রেখে কোথাও যায় না।
গত রাতে যা মুলামের সামনে ঘটেছে তার কোন ব্যাখ্যা নেই।
গভীর ঘুমের মাঝে চেঁচিয়ে ওঠে আফসানা। ওই দেখো।
মুলাম ঘুমের মাঝে আঁতকে জেগে চোখ মেলে। ওটা কী? দুজনেই দেখল তীব্র সবুজ আলোর একটা সাপ জড়িয়ে আছে খাটের মশারি স্ট্যাণ্ডের সাথে, আফসানার পাশে। এরকম দ্যুতি ছড়ানো সাপ এর আগে কেউ দেখেছে কি না জানা নেই ওদের।
এ বাড়ির তিনটা প্রাণীই বুঝে গেছে এখানে অদ্ভুত সব ঘটনা ঘটছে।
আফসানা বাপের বাড়ি যেতে চাইলে মা-ছেলে দুজনেরই মন খারাপ হয়ে যায়। আর আফসানারও অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে। ওদের ছাড়া একবেলাও সে থাকতে পারে না। এখন। দিনের আলোতেও ঘটে চলেছে অদ্ভুত সব ঘটনা।
কাল দুপুর বেলা, আফসানা ঘুমাচ্ছিল মুলামের কোলের মধ্যে। হালকা ঘুমে নিজের কানে শুনল কেউ একজন নিচু স্বরে ওর মাথার কাছে বলে চলেছে…।
আঙুল ভাজা খাবা, খাবা আঙুল ভাজা, খাবা-খাবা! এত ভারী শরীরটা নিয়ে ওর চলাফেরা করা কঠিন। সারাদিন ধরতে গেলে বিছানায়ই থাকে। মুলামের দূর সম্পর্কের এক ফুফু এসেছে। সে-ই আফসানাকে দেখাশোনা করে।
আট
গত রাতে জানালার পাশে মাথাটা আবার দেখেছে আফসানা। ওর প্রসবের দিন ঘনিয়ে আসছে। কাল গ্রামের একমাত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রী জোবায়দা এসে দেখে গেছে। বলেছে বাচ্চা ভাল আছে। বাচ্চার আকার বেশ বড় গ্রামে সাধারণত ছোট আকারের বাচ্চাই হয়। এত বড় বাচ্চা বাড়িতে প্রসব নিয়ে সে মনে-মনে একটু শঙ্কিত হলেও ওদেরকে কিছু বুঝতে দেয়নি।
আজ তিন দিন ধরে একটানা বৃষ্টি চলছে। মুলাম কোথা থেকে জাল বোনা শিখেছে। সারাদিন ঘরের দোরে বসে বউকে পাহারা দেয় আর জাল বোনে। যে সুচ দিয়ে জাল বোনা হয় স্থানীয় ভাষায় তাকে নলী বলে। ওরকম একটা ঝুলছিল খাটের রেলিঙে। আফসানা বিছানায় শুয়ে থাকে সারাদিন, কেবলি চোখটা বুজে এসেছিল। হঠাৎ খেয়াল করল। নলীটা একা-একাই নেমে আসছে ওর দিকে। সোজা এসে ওর হাতে ইঞ্জেকশনের মত ঘঁাচ করে ঢুকে গেল। চিৎকার করে বসে পড়ল ও।
সর্বনাশ! এ কী অবস্থা! বিস্ময়ে হতবাক মা-ছেলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। সারা বিছানা ভেজা। পানি যা ছিল, সব ভেঙে গেছে। বাইরে তুমুল বর্ষণ। মুলাম ছুটল জোবায়দার কাছে।
জোবায়দা এসে একখানা ইঞ্জেকশন দিল। ব্যথায় কুঁকড়ে যাচ্ছে আফসানার শরীর। চেঁচিয়ে বলল, একটু আগে নলী
এসে আমাকে ইঞ্জেকশন দিল, এখন আবার তুমি?
কিছু বুঝল না জোবায়দা। সাধ্যমত চেষ্টা করে চলেছে। ও। কিন্তু রোগীর অবস্থা ক্রমশই জটিল হচ্ছিল। এক সময় জোবায়দা আত্মসমর্পণ করল।
খালাম্মা, আফসানার অবস্থা ভাল না। ওর সদরে নিয়ার চিষ্টা করেন। বাচ্চা অনেক বড়, তারপর পানি সব ভাঙে গেছে। বাচ্চা বাঁচে আছে কি না বুঝতিছিনে। এখন ওকে বাঁচাতি হবি।
ও, মা, আমার সানারে বাঁচাও, ও মরে গিলি আমি কিন্তু মরে যাব, বিলাপ করতে থাকল মুলাম।
ও রে, মুলাম, শিগ্গির সরাইল লোক পাঠা, ওর বাপ মারে খবর দে। দুই মা-ছেলে মরা কান্না জুড়ে দিল। ওদিকে আবহাওয়া চরম রূপ নিল।
সন্ধ্যায় আফসানার বাবা-মা এলেন। ধাইমা গুলজানকে সঙ্গে করে। সে দুই-চার গ্রামের অভিজ্ঞ ধাত্রী। আফসানার ভাইবোনরা সবাই তার হাতেই জন্মেছে।
প্রায় সংজ্ঞাহীন পড়ে আছে আফসানা। ওদিকে দুজন ধাত্রীর অবিশ্রান্ত চেষ্টা চলছে বাচ্চা খালাসের।
দুর্ঘটনাটা ঘটল গুলজানের হাতেই। প্রায় খালাস হয়েই এসেছিল। যদিও বাচ্চা মারা গিয়েছিল আগেই। অতিরিক্ত টানাটানিতে হঠাই ছিঁড়ে এল মাথাটা!
নয়
আফসানার বাঁচার আশা ক্ষীণ। ইতোমধ্যেই মরা কান্না শুরু হয়ে গেছে বাড়িতে। প্রকৃতিও আফসানার শোকে যেন কেঁদে চলেছে নিরন্তর। আঁদরের পুত্রবধূর এ অকাল মৃত্যুর সম্ভাবনা মানতে চায় না রওশনআরা। সারা জীবন সে মানুষের জন্য করে গেল আর তারই কি না এত শাস্তি। বিরূপ আবহাওয়ায় ডুবে গেছে রাস্তাঘাট। নিকষ কালো রাত। তখন এমনিতেই তেমন কোন যানবাহন ছিল না ঘোড়াগাড়ি ছাড়া। রাস্তাঘাট ডুবে যাওয়ায় ঘোড়াগাড়ি চলা অসম্ভব।
খাঁটিয়ায় তোলা হলো আফসানাকে। রওশনআরার মত। তার একই কথা, বাঁচাতেই হবে আফসানাকে।
গ্রামের সবচেয়ে শক্তিশালী কয়েকজনকে জোগাড় করা হলো। মড়ার খাঁটিয়া বহনের জন্য। প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে দেয়া হলো খাটখানা।
খাঁটিয়া চলল মৃতপ্রায় আফসানাকে নিয়ে। পিছনে সব আপনজনেরা। অঝর বৃষ্টি। পথঘাট কাদা-পানিতে মাখামাখি। সবার মাথায় ছাতা, হাতে হারিকেন। গ্রামসুদ্ধ মানুষ চেয়ে থাকল। যেন নিশুত রাতের শবযাত্রা চলেছে…
.
চার দিন পর রোদ উঠল সেদিন। ছিন্ন মাথাটা সমাধিস্থ করা হলো নাদুরিয়া গোরস্থানে। খবর এল, আফসানার জীবন শঙ্কা কেটে গেছে। শিশুটার দেহটা ওখানে গিয়ে সহজেই বের করা। হয়েছিল। ছেলে শিশু ছিল ও। কোন অপারেশনও করতে হয়নি। পরে দেহটাকে সমাধিস্থ করা হয় রাজবাড়ি গোরস্থানে। মড়ার খাঁটিয়া থেকে মৃতপ্রায় আফসানা ফিরল জীবন নিয়ে।
কয়েক বছর পর মুলাম আফসানাকে নিয়ে পাড়ি জমাল ঢাকায়।
দশ
গল্প শুনতে-শুনতে ইনায়া ঘোরের ভেতর চলে গিয়েছিল।
নানু, আফসানা তো তুমি? আর আমার নানুভাই মোত্তালিব হোসেন, তার নাম মুলাম? জানো, নানু, তোমার গল্প শুনে আমি কাঁদছিলাম, তার জন্য খুব মায়া লাগছিল! যাকে আমি দেখিনি, সে-ই তো তোমাকে বাঁচাল। তোমার শাশুড়ি মানে নানাভাইয়ের মা, তাই না? খুব খারাপ লাগছে, আমি তাকে দেখতে পেলাম না, বলল ছোট্ট ইনায়া।
হ্যাঁ, তিনি তোমার বড়মা। আর আমার দ্বিতীয় জনম দেয়া মা ছিলেন। বলে চোখ মুছল আফসানা।
সত্যি তোমাদের জীবন কী কঠিন ছিল!
তোমার ভয় লাগেনি, নানুয়া? প্রশ্ন করলেন আফসানা।
একদম না, বরং মামার মাথাটা দেখতে ইচ্ছে করছে। সে বেঁচে থাকলে তো তৌসিফ মামা সহ আমার আরেকটা মামা থাকত। অদ্ভুত তুমি, কী করে ভেঁড়া মাথাটা তুমি আগেই দেখতে, তার মুখে মা ডাক শুনতে?
এগারো
আজ রাতটাই আছে ইনায়ারা। সকালেই রওনা হবে ঢাকা। ওর মা তানতা ফিরবে আগামীকাল।
বাইরে রুপোর থালার মত একাদশীর চাঁদ উঠেছে। দোতলার ওপর দক্ষিণে খোলা বিশাল শোবার ঘরখানা। নানা, নানুর মাঝেই শোয় ইনায়া। ওরা দুজন নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। ইনায়ার ঘুম নেই। ও শুধু নানুর ছোট বেলার গল্পটার কথা ভাবছে। হঠাৎ থপথপ শব্দ! ইনায়ার একটু ভয়-ভয় লাগল। বুকের ওপরের লেপটা মুড়ি দিতে টান দিল। এ কী, একটা মাথা! প্রায় ওর বুকের কাছে! বুঝতে বাকি রইল না ওর, এটা কার মাথা, ও তো দেখতেই চেয়েছিল। বেশ কিছুক্ষণ অপলক তাকিয়ে থাকল ওটার দিকে। একসময় চিৎকার করে উঠল ও। নানা-নানু জেগে গেল, জড়িয়ে ধরল। ইনায়াকে।
তুমি কেন ওকে এসব গল্প বলতে গেলে? একটু রেগেই বললেন মুত্তালিব হোসেন।
সরি! নানুয়া আমার, বলেছিলাম তুমি ভয় পাবে।
না, নানু, আমি তেমন ভয় পাইনি। আমি সত্যি মামার মাথাটা দেখেছি। স্পষ্ট চাঁদের আলোয়। তুমি যে বলেছিলে? চিনে পুতুলের মতই। আমার লেপের ওপর। তবে একটু ময়লা ছিল। তুমি বিশ্বাস করো।
বারো
সব গোছানো চলছে, আজই ওরা ঢাকা রওনা করবে। বিছানা থেকে ইনায়াকে উঠিয়ে দিলেন আফসানা। সব ঝেড়ে লেপ কম্বল গোছাচ্ছিলেন।
এ কী? বলে অবাক হয়ে মেলে ধরলেন ধবধবে সাদা লেপটা। দেখো, লেপের কভারে এটা কীসের দাগ?
মুত্তালিব আর আফসানা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন নিজেদের দিকে। সাদা ধবধবে লেপটার ওপর গোল-গোল ময়লার ছোপ। লেপের ওপর যেন কোন গোল ময়লা কিছু গড়িয়ে গেছে।
চোখ ভিজে উঠল আফসানার! বুঝতে বাকি রইল না। ছোট্ট ইনায়া ভুল দেখেনি।
কালের গর্ভে বিলীন সময়, আত্মা অবিনশ্বর!
এ মায়ার ভুবন, কত কী খেলেন ঈশ্বর,
যুক্তিতে তার মেলে কি তাবৎ উত্তর??
ছায়াশরীর – অরুণ কুমার বিশ্বাস
একতারিনা টেই আমার সঙ্গে পড়ে। লণ্ডন স্কুল অভ বিজনেস, মানব-সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এমএস করছি। মেয়েটা বুদ্ধিতে স্প্যানিশ, মেজাজে আইরিশ, আর দেখতে ইণ্ডিয়ানদের মত। ভীষণ রগচটা একতারিনা। আমি তাকে কখনও একতা, আবার কখনও বা রিনা নামে ডাকি। ও ফিক ফিক করে হাসে। জানতে চায়, একতা বা রিনা নামে আমার কোনও গার্লফ্রেণ্ড আছে কি না।
একতা বা রিনাকে ক্লাসে কেউ তেমন পছন্দ করে না। কারণ ও আইরিশদের মত গোঁয়ার। রেগে গেলে বদলে যায় ওর মুখচ্ছবি। যেন ঠেলে বেরিয়ে আসে লালমুখো মেয়েটার চোখের মণিদুটো। এত বেশি রেগে যায় যে, ওর গলা থেকে যা বেরোয়, তাকে মোষের গাঁক-গাঁক বা বাঘের হক বলেও ঠিক বোঝানো যাবে না। তবে আমি জানি, একতা মেয়েটা নেহায়েত মন্দ নয়। সহপাঠী হিসেবে ও আমাকেই যা একটু মান্যিগণ্যি করে। ক্লাস মিস গেলে আমার কাছে হেল্প চায় একতারিনা।
ওর গায়ের রঙ সাহেব-সুবোদের মত উজ্জ্বল নয়। বরং এশীয়দের মত খানিক শ্যামলিমা আর হরিদ্রাভের মিশেল আছে। হঠাৎ একদিন একখানা ফ্যামিলি ছবি এনে একতা বলল, দেখো তো, নীল, এই ছবিতে কজন মানুষ দেখা যাচ্ছে? ভাল করে, খুব মনোযোগ দিয়ে দেখবে। ব্যাপারটা সিরিয়াস।
পুরুষানুক্রমে ধনী পরিবারের মেয়ে একতা। যখন যা মন চায়, তখনই তা পেয়ে যায় সে। একতা সেদিন আমাকে ইউনি থেকে ওর স্ব-চালিত বিএমডব্লিউতে তুলে নিয়ে সেন্ট্রাল লণ্ডনের গ্রিনপার্কে এনে ফেলল। খেয়ালি মেয়েটার যখন রোখ চাপে, তখন কারও কথা খুব একটা কানে তোলে না। সত্যি কথা বলতে, মাঝে মাঝে খুব বিরক্ত হলেও ওর দুচোখে নিপাট সারল্য আমাকে আবিষ্ট করে। তাই সব মুখ বুজে সয়ে যাই। আপনারা একে যদি বন্ধুত্ব বলেন, তবে বন্ধুত্ব, প্রেম বললে প্রেম। আসলে একতাকে আপাতত প্রশ্রয় না দিয়ে বুঝি আমার নিস্তার নেই। আর এই ছায়াসঙ্গিনীর মূল রহস্যও সেখানেই।
শীতের শুরুতে হরদম পাতা ঝরছে গ্রিনপার্কে। আবার মাঝে মাঝে ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ছাতিম গাছের মত দেখতে লণ্ডন প্লেনের নিচে বসে ছবিটা দেখছি। একতা নন-স্টপ ওয়াকার্স চিপস চিবাচ্ছে। সঙ্গে ঢকঢক করে গিলছে ব্লুবেরি ফলের জুস।
আমি ছবিতে বুদ। একতা যখন বলছে সিরিয়াস, তখন গম্ভীর না হয়ে উপায় নেই। যথাযথ গুরুত্ব না দিলে রেগে গিয়ে হয়তো আমার মাথায় মারবে গাট্টা। ছবিতে দুজন মাত্র মানুষ, ব্যাকগ্রাউণ্ডে শহরের কোনও গ্রেভইয়ার্ডের ছবি। বেশ পুরনোই মনে হয়। ছবি ও শশ্মশান-দুটোই পুরনো।
জায়গাটা কোথায়? একতার চোখে চোখ রাখলাম আমি।
অনুমান করো। অনেক দিন হয় তুমি লণ্ডনে আছ, নীল। ইউ মে গেস! উল্টো প্রশ্ন ছুঁড়ল একতারিনা।
বেকুবের হাসি হাসলাম। কারণ লণ্ডনে পড়তে এসে আর যাই হোক, কবরখানার ব্যাপারে মোটেও উৎসাহ বোধ করিনি। রহস্য ভালবাসি এ কথা ঠিক। জানি না, তুমি বলো, আমি হার স্বীকার করে নিলাম।
একতা তাও সঠিক উত্তর দিল না। বলল, ছবির পটভূমি কোন্ গ্রেভইয়ার্ড, ওটা তোমার গবেষণার বিষয় নয়, নীল। দয়া করে বলল, এই ছবিতে কটা মানুষের অবয়ব দেখছ।
কেন, দুজন! একজন পুরুষ, অপরজন মহিলা। এ নিয়ে গবেষণার কী আছে! ক্রমশ আমার স্বরে উত্তাপ বাড়ছে। মেয়েটা পেয়েছে কী! বাঙালি বলে আমার মেজাজ-মর্জি খুব যে শীতল, তা কিন্তু নয়।
বর্ণময় লণ্ডন প্লেনের একটা পাতা সহসাই খসে পড়ল একতার চুলে। যেন ঠিক। প্রজাপতির মত। মেয়েটা হেঁয়ালিমাখা হাসি উপহার দিল। সত্যি, বিলেতি বিকেলে বড় মোহময় লাগে মেয়েটাকে। একতা সুন্দর, অপাপবিদ্ধ চাহনি ওর। একতার সব ভাল, শুধু ওই আইরিশ মেজাজটা ছাড়া।
ও শ্লেষের সুরে বলল, তুমিও পারলে না! ভেবেছিলাম তুমি পারবে। কারণ তুমি বাঙালি, তোমরা বুদ্ধিমান। এখন দেখছি তুমিও গড়পড়তা মানুষের মত। তলিয়ে দেখার ক্ষমতা বা চোখ তোমার নেই। তুমি হেরে গেলে, নীল, তুমি অ্যাভারেজের দলে।
কথাটায় খোঁচা আছে, বেশ বুঝতে পারি। কিন্তু অসহায়ের মতো কিল খেয়ে কিল চুরি করতে হলো। কারণ ছবিতে দুজন মানুষের ছবি ছাড়া সত্যি আর কিছু দেখতে পাইনি যে! ছবিটা খানিক আবছাও। যদূর মনে হয়, কোনও এক শহুরে কবরখানায় সাঁঝের মুখে উবু হয়ে বসে আছে দুজন মধ্যবয়সী নারী-পুরুষ। পটভূমি আবছা, তাই ভাল বোঝা যায় না।
এরা কারা, চিনতে পারো? একতার পরবর্তী প্রশ্ন।
সম্ভবত তোমার কোনও রিলেটিভ, সেফ সাইডে থেকে উত্তর দিলাম। নতুন করে অ্যাভারেজ মার্কস পেতে চাইনি।
এটা কোনও উত্তর হলো না। বি মোর স্পেসিফিক। নইলে ফুল মার্কস পাবে না।
তোমার বাবা-মা, কিছু না বুঝেই বললাম।
হলো না। তুমি একটা বুন্ধু। গ্রেভইয়ার্ডের ক্রুশচিহ্ন বা দেয়ালের গায়ে সাঁটা মার্বেলের স্থাপত্য লক্ষ করেছ! ওটা অন্তত এক শ বছরের পুরনো। এ জাতীয় মার্বেল এখন আর বাজারে নেই। সময়ের বিবেচনায় কী করে ছবিটা আমার বাবা-মায়ের হবে!
তা হলে তোমার গ্র্যানি-গ্র্যানপার নিশ্চয়ই, আমি একের পর এক আঁধারে ঢিল ছুঁড়ে যাচ্ছি।
ইয়েস, নীল, ওটা আমার দাদা-দাদির ছবি। আর কবরে শুয়ে আছেন সম্ভবত আমার গ্রেট-এ্যানি।
ইচ্ছে করেই সম্ভবত শব্দটার উপর বিশেষ জোর দিয়েছে একতা। আমি এর কারণ জানতে চাইলে ও যা বলল, সেটা মেনে নেয়া আমার পক্ষে সত্যি কঠিন। কারণ পুরোপুরি একজন ডাউন-টু-আর্থ অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ ও বাস্তববাদী মানুষ আমি। কোনও রকম, হেঁয়ালি বা অবাস্তবতা মেনে নিতে প্রস্তুত নই।
একতা জানাল, ছবিটার ওই কবরে আদৌ আমার গ্রেট এ্যানি (দাদিমার মা) শুয়ে আছেন কি না, কেউ জানে না। তুমি বরং ছবিটা নিয়ে যাও। সময় নিয়ে ভাল করে দেখো। তা হলেই বুঝবে আমি কী বলতে চেয়েছি।
একটু রাগত স্বরেই জানিয়ে দিই আমি, সে না হয় দেখব। তুমি শুনে রাখো, একতা, আমি কিন্তু ভূত-ফুত কোনও কিছুতে বিশ্বাস করি না। তাই আমাকে প্লিজ গাঁজাখুরি গপ্পো শোনাতে এসো না। তাতে লাভ হবে না কিছু।
এর উত্তরে একতা আমার দিকে এমনভাবে তাকাল, যেন মারাত্মক ভুল কিছু বলেছি। চরম অন্যায় করেছি। এবং এর ফল আমাকে হাতেনাতে পেতে হবে।
একতা কষ্ট পেয়েছে ঠিক, কিন্তু তাতে আমার বয়েই গেল! সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে এখানে এসেছি একটু এগিয়ে যেতে, ভূত-প্রেতের বিশিষ্ট গবেষক হিসেবে নিজেকে বিশ্বদরবারে হাস্যকর করার জন্য নয়। আমি যথারীতি ডেরায় ফিরলাম। একতার বিএমডব্লিউ আমাকে ড্রপ করে দিল। এর ঠিক দুদিনের মাথায় দুটো ঘটনা ঘটল। দুটোই আকস্মিক এবং যারপরনাই অবাস্তব।
সানডে টাইমস ট্যাবলয়েডে খবর বেরোল, ইউকের অন্যতম শরিক দেশ ওয়েলসের এক শহরে গরিক কাসল নামে একটি জায়গা আছে। সেই পুরনো দুর্গে কাল রাতে মহিলা ভূত বা প্রেতিনী দেখা গেছে। কয়েকজন প্রত্যক্ষ করেছে এই ঘটনা। এ খবরের পুরোটাই সত্যি, একটুও মিথ্যের মিশেল নেই।
এই অব্দি ঠিক ছিল। এ কথা কে না জানে, ভূত-প্রেত বিষয়ক গালগপ্পোর আদি নিবাস তথাকথিত পশ্চিমা বিশ্ব। ইউরোপিয়ানরা ভূতের গপ্পো পেলে স্ত্রীকে আদর করতে ভুলে যায়। গপ্পে যথেষ্ট রস পেলে পেটের খিদেও থাকে না। বিলিতিরা ভূত দেখবে, তাতে আর আশ্চর্য কী! কিন্তু সানডে টাইমস্ সবিস্তারে লিখেছে, উইলি কেভিন নামের সেই ভদ্রলোক (নাকি ভূতলোক) প্রেতিনী দেখে তার ছবিও তুলেছেন। সেই তরতাজা ভৌতিক ছবি ছেপেছে পত্রিকাটি। ক্ষণভঙ্গুর গরিক কাসলের জরাজীর্ণ কার্নিশে দেখা যাচ্ছে এক অল্পবয়সী মেয়ের ছবি। দেখতে অবশ্য সাধারণ মানুষের মত নয়, মেয়েটির ঠোঁটে কাঁচা-রক্তের আভাস আছে। ব্যস, তামাম গ্রেট ব্রিটেন এই খবরে পপকর্নের মত সোৎসাহে ফুটতে শুরু করেছে। সবার আগে ব্যাপারটা আমার নজরে : আনল মিস একতারিনা, আমার বন্ধু।
কী, এবার বুঝলে, নীল, তোমার-আমার হিসেবের বাইরেও কিছু আছে! সানডে টাইমস্ তো আর ভুল ছাপেনি! একতার কণ্ঠে স্পষ্ট ব্যঙ্গ।
বিলক্ষণ! সানডে টাইমস্ কখনও ভুল ছাপতে পারে না। কিন্তু ওই ফটোগ্রাফার উইলি কেভিন নামের লোকটা তোমার কোনও আত্মীয় বুঝি! তুমি চাইলে আর অমনি সে একখানা জলজ্যান্ত ভূতের ছবি তুলে ছেপে দিল! ইচ্ছে করেই একতাকে খানিক খোঁচালাম।
তুমি কী বলতে চাও, নীল! আমাদের পত্রিকাঅলারা স্রেফ স্টান্টবাজি করে চলে? দে হ্যাভ রিয়েলি সামথিং টু শেয়ার উইদ আস!
অফকোর্স। খবরটা মিথ্যে, তা তো আমি বলিনি। জাস্ট বলতে চাইছি, বেচারা কেভিন ক্যামেরা নিয়ে সেজেগুজে কী করে ভূতের দেখা পেল! ভূতের সঙ্গে আগে থেকেই তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল বুঝি!
ব্যস, এতেই খেপে ঝাল বেচারা একতারিনা। বগুড়ার ধানিলঙ্কা চিবানোর মত ফুঁসতে লাগল। আমি নাকি ওদের দেশের ভূতদের অপমান করেছি। এ অপরাধ নাকি ক্ষমার অযোগ্য। ওর বক্তব্য, এ অন্যায়ের কোনও রেয়াত হয় না। যাঁদের আমি অপমান করেছি, সেই ভূতগণ নিজেরাই আমাকে। চরম শিক্ষা দেবে।
এর পরের ঘটনাটা একটু অন্যরকম।
হাস্যকর নয়, ভয়ঙ্কর।
ভূতের ভুয়োমির বিষয়ে আমি এতকাল মোটামুটি নিশ্চিত ছিলাম। রাতের ব্যাপারটা আমাকে বড় কাহিল করে দিয়েছে। রাত তখন বোধ হয় একটা-দেড়টা হবে। লণ্ডনের বাঙালি এলাকা ব্রুকলেনের পেটিকোট মার্কেট থেকে ফিরতে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেছে আজ। সন্ধ্যায় ভারী নাশতা করেছি, তাই ডিনারের তাড়া নেই। তা-ও বাসায় ফিরে শুতে যাবার আগে কফিসহযোগে মেক্সিকান টোস্ট খেলাম। বাইরে শীতের প্রাবল্য, তাই শহর লণ্ডন আজ আগেভাগেই সুনসান হয়ে গেছে। ঠাণ্ডায় জবুথুবু, শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য। রেডিয়েটরের তাপ-নিয়ন্ত্রক চাবিটা খানিক চাগিয়ে দিলাম। তারপর বিছানায় আধশোয়া হয়ে বসলাম একতার দেয়া ছবিটা নিয়ে। দেখিই না এতে কী আছে!
ছবি যেন শুধু ছবি নয়!
আশ্চর্য! দিনের বেলা যা চোখে পড়েনি, এখন তা দিব্যি স্পষ্ট ধরা দিল! ..
শেড়অলা টেবল-ল্যাম্পের মরা আলোয় ছবিটা যেন অন্যরকম মনে হলো! একতা বারবার জানতে চাইছিল দুজন মানুষের বাইরে ছবিতে আর কিছু দেখা যায় কি না! ছবিটা খুব স্পষ্ট নয়, আগেই বলেছি। বরং বেশ হেইজি! কিন্তু তা-ও বুঝতে অসুবিধা হয় না, ছবিতে দুজন মানুষের ঠিক পেছনে আরও একজন। একটা অবয়ব যেন উঁকি দিচ্ছে। এই তৃতীয় মানুষটি কে!
এক থুথুরে বৃদ্ধার ছবি বলে ভ্রম হলো। ভ্ৰম, নাকি সত্যি! শীর্ণ দেখতে, লোলচর্ম। বয়স আন্দাজ করা যায়, অন্তত নব্বই। একতা বলেছিল, তার গ্রেট-এ্যানি মারা যান বেশ বয়সে। কেমন করে মারা গেছেন, বা তার স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল কি না, তা সে বলেনি। এমনও হতে পারে, একতা সে কথা জানেই না।
কবরখানায় ভোলা ছবিটায় এই তৃতীয় ব্যক্তির অস্তিত্ব ক্রমশ প্রকট হলো। তিনি যে একতার পূর্বসুরি, বুঝতে অসুবিধা হলো না। চেহারায় মিল আছে। কেমন এক অদ্ভুত নেশার ঘোরে বারবার ছবির দিকে তাকাতে বাধ্য হলাম। ছবি থেকে চোখ সরাতে পারছি না। সহসা ব্ল্যাক-আউট, লণ্ডনে যা এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। নাকি আমার টেবল-ল্যাম্পের ফিউজ কেটে গেল! চারপাশে প্রগাঢ় আঁধার, অপলক চেয়ে থাকি একতার দেয়া ছবিটার পানে।
সে কী! আমার আশপাশে টের পাই কারও অস্তিত্ব। পায়ের আওয়াজ, নিঃশ্বাসের শব্দ, কিংবা মৃদু অথচ অনুভবযোগ্য আনাগোনা! ভুল শুনছি না তো! সহসাই মনে পড়ল সানডে টাইমসে পড়া গরিক কাসলের সেই প্রেতিনীর কথা। চোখের পাতে কারও ছায়া ভাসছে বুঝি! একতার ছবিতে ছায়াবয়ব আর ওয়েলসের গরিক দুর্গের কার্নিশে ঝুলে থাকা অশুভ অস্তিত্ব আমার সামনে নিমিষেই একাকার হয়ে গেল। বুঝলাম না, আমি সত্যি জেগে আছি, নাকি স্বপ্ন দেখছি কোনও!
অথচ ছবির পেছনের ওই ছায়াশরীরের সঙ্গে একতার চেহারার দারুণ মিল। মনে হয় যেন ওটা একতার ভবিষ্যৎ অবয়ব। আরও বয়স হলে ও দেখতে এমনই হবে।
মনে হলো, একতাকে সেলফোনে ট্রাই করি। জানতে চাই, ওর গ্রেট-এ্যানি দেখতে ঠিক কেমন ছিলেন! একটু আগে যেমন দেখলাম, সে-রকম কি না! বা আদৌ কাউকে দেখেছি কি! পুরোটাই বিভ্রান্তি নয় তো! সন্ধের নাশতাটা বেশ ভারি হয়ে গিয়েছিল আজ! ঝলসানো হরিণের মাংস আর পেশোয়ারি পরোটা। তারপর ভরপেট সফ্ট ড্রিঙ্কস, ক্যাডবেরি চকলেট ডজনখানেক। চকলেট এখানে ভারি সস্তা।
এর পরের ঘটনা বিশ্বাসের অতীত, বলা যায় ঐন্দ্রজালিক। কাউকে বিশ্বাস করানো যাবে না, কারণ আমি নিজেই এ ব্যাপারে নিশ্চিত নই। তবে ঘটনাটা ঘটেছে, আমার চোখের সামনেই। সিইং ইয বিলিভিং। বিশ্বাস না করে উপায় কী!
পরদিন আলো ফুটতেই একতার ওয়েস্ট হ্যাম্পস্টেডের বাসায় গিয়ে হাজির হলাম। সেন্ট্রাল, সার্কেল ও মেট্রোপলিটন-তিনখানা টিউবলাইন বদল করে অনেকটা পথ গেলে একতার বাসা। এখানেই থাকতেন বিখ্যাত রোমান্টিক কবি জন কিট্স্। হ্যাম্পস্টেড হিথের বাড়িতেই এক উইলো গাছের নিচে বসে কিটস্ লিখেছেন তাঁর মোস্ট ফেমাস গীতিকবিতা: অড টু নাইটিঙ্গেল। এসব কথা এমন আমাকে বলেছে। ওর দাদার সঙ্গে কিটসের বাবার খুব খাতির ছিল শোনা যায়। শুনে আমার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে যায়। জন কিটস্ কত বড় মাপের কবি! তিনি লিখেছেন, বিউটি ইয টুথ, টুথ ইয বিউটি। কিংবা আ থিং অভ বিউটি ইয জয় ফরএভার। বিশ্ব-সাহিত্যে সত্য ও সুন্দরের এমন বিশ্বস্ত উপাসক আর হয় না।
একতা বাড়িতে নেই, আমি হতাশ। ভোরে নাকি বেরিয়ে গেছে। কখন ফিরবে, কেউ বলতে পারে না। অথচ একটা প্রশ্ন তাকে আমার করতেই হবে। উত্তর না জানা অব্দি শান্তি নেই। ওর সেলফোন বন্ধ, নরমালি যেমন থাকে। এমন বিরক্তিকর মেয়ে আর হয় না। মেজাজ-মর্জি কখন বিগড়াবে, বোঝার উপায় নেই।
একটা চিরকুট রেখে এলাম একতার বাসায়। এসেই যেন আমাকে কনট্যাক্ট করে। ব্যাডলি নিডেড। কিন্তু তাতেও মনের শান্তি নেই। পাশেই টেকো এক্সপ্রেস থেকে টিউনা স্যাণ্ডউইচ ও কন্টিনেন্টাল বিনস দিয়ে নাশতা সারলাম। তারপর নিরন্তর প্রতীক্ষা। জানতেই হবে, একতার দেয়া। ছবিতে যে গ্রেভইয়ার্ড দেখা যাচ্ছে, ওটা কোথায়। আই নিড টু ভিযিট দ্য প্লেস! আরজেন্টলি। কে সে, কাল গভীর রাতে যে আমার বেডরুমে প্রবেশ করেছিল!
অবশেষে একতাকে যখন পাওয়া গেল, তখন নেমেছে। রাত। শীতের দাপট আজ আরও বেশি। ঠাণ্ডায় দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। হাঁটুও যেন কথা শুনছে না। পা পিছলে যাচ্ছে। হিমাঙ্কের নিচে তাপমাত্রা। ডিসেম্বরের শেষ দিকে লণ্ডন শহর স্রেফ দোজখ। বিশেষত শীতকাতুরে এশীয়দের জন্য। বলা বাহুল্য, আমি তাদের দলে।
মধ্য লণ্ডনের ওয়ারেন স্ট্রিটে একতারিনার সঙ্গে মোলাকাত হলো আমার। ও তখন ঝোড়ো কাক। এই মেয়েকে আমি চিনি না। চোখ বসে গেছে, ঘোলাটে, চাহনি, কণ্ঠস্বরও বদলে গেছে। ও বলল, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি, নীল। ভাল, তুমি এসে পড়েছ।
কেন, বলো তো?
আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে। তুমি যাবে আমার সঙ্গে? আশা করি আমাকে নিরাশ করবে না, নীল, একতার কণ্ঠে অনুনয়।
জেদি গলায় আমি বললাম, আমিও একখানে যেতে চাই যে! আজই, এক্ষুণি। আমার যে আর কোনও উপায় নেই। এই রহস্য ভেদ না হলে আমার চোখে ঘুম আসবে না।
কোথায় যাবে?
তোমার দেয়া ছবির পটভূমি, সেই কবরখানায়, হিস হিস করে বললাম।
শুনে ও এমন চমকাল, বলার নয়!
অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল একতা। বলল, কী আশ্চর্য! আমিও যে গ্রেভইয়ার্ডের কথাই ভাবছিলাম। ইনফ্যাক্ট, সারাটা দিন আমি ওখানেই ছিলাম।
ফিরে এলে কেন তবে?
কারণ তোমাকেও সঙ্গে চাই। রাতটা বড় নিরাপদ নয়।
তার মানে তুমি ভয় পাচ্ছ, তাই না, একতা! মওকা পেয়ে জবরদস্ত খোঁচা দিয়ে ফেললাম। প্রতিটি পুরুষ জীবনে একবার অন্তত তার অপমানের বদলা নিতে চায়। আমিও সুযোগটা লুফে নিলাম। তখনও জানতাম না, কী ভয়ঙ্কর চমক অপেক্ষা করছে আমার সামনে।
একতা এসব গায়ে মাখেনি। বরং কঠিন নৈর্ব্যক্তিক সুরে বলল, আমাকে সেখানে যেতে হবে। তুমি যাবে কি না বলো। না গেলে আমি একাই যাব। যাবই।
ওর কণ্ঠের কাঠিন্য আমাকে তাড়িত করল। কেন যেন মনে হলো, কোনও সর্বনেশে পথে এগোচ্ছি আমরা। আমি ও একতা এক অমোঘ নির্দেশে ছুটে চলেছি নিরুদ্দেশের দেশে।
কবরখানা কোথায়, জানতে পারি?
জেনে কী লাভ! তামাম লণ্ডনের কতটুকু তুমি চেন! তা ছাড়া, জায়গাটা শহরের চৌহদ্দির ভিতরে নয়, বলা যায় শহরতলী, বা খানিক গ্রামের দিকে।
তাও বলো, জানা থাকলে ক্ষতি কী!
একতা দুর্বোধ্য সুরে বলল, ককফস্টার ফার্মহাউস। ওখানে বক্সহিল বলে একটা জায়গা আছে। একটা পাহাড়, দেখতে বাক্সের মত চৌকো। খুব নিরিবিলি আর সুনসান। যেন কোনও ফিউনেরাল অনুষ্ঠানে বাইবেল পড়ে শোনাচ্ছে।
কখন যাচ্ছি আমরা?
এখনই। নো ওয়েস্ট অভ টাইম। একতার যেন আর তর সইছে না।
লীলায়িত বিএমডব্লিউ চেপে আমরা যখন রওনা হলাম, তখন নেমেছে রাত। লাল-নীল হাজারো রঙে সয়লাব শহর লণ্ডনের অলিগলি। এই শহরের কিছু কিছু রাস্তা এত চাপা, গলি বলেও ঠিক বোঝানো যায় না। এখানে গাড়ির গতি সীমিত। মাখনের মত গলে বেরিয়ে যায় গাড়ি, সড়ক দুর্ঘটনার কেস নেই বললেই চলে।
লণ্ডনের দক্ষিণ-পশ্চিম ছুঁয়ে বেড়ে ওঠা কিউ গার্ডেনের ছায়াসুনিবিড় বুনোপথ ধরে সামনে এগোই।
একতারিনা গাড়ি ভালই চালায়। অটো গিয়ার, সুদলি সাঁই-সাঁই করে বাতাস কেটে পেরিয়ে যায় মাইলের পর মাইল। আমাদের দেশের হাইওয়েকে এখানে বলে মোটরওয়ে। কোনও ঝাঁকুনি নেই, কারণ এখানে হাডে পারসেন্ট কাজ হয়। ঠিকাদাররা ঠকবাজি করে না। তাদের বাড়তি পারসেন্টেজ গুনতে হয় না।
প্রায় ঘণ্টা দেড়েক যাবার পর থামল একতা। গাড়ি পার্ক করল বুনো রাস্তার ধারে।
কী ব্যাপার, থামলে কেন! এসে পড়েছি বুঝি?
নো, ডিয়ার! সবে সন্ধে। এখনও অনেকটা বাকি।
চলো তা হলে, এগোই।
যাবো তো। তবে তার আগে গলাটা একটু ভিজিয়ে নেয়া দরকার। হেভি টেনশান হচ্ছে। গাড়ির খাবার পেট্রলও নিতে হবে।
রোডসাইড ইন।
বা ওটাকে পাব বলতে পারেন। নামখানা জবরদস্ত, ফ্যান্টম বারমেড। গা-ছমছমে পরিবেশের সঙ্গে খাপে খাপ মিলে যাচ্ছে। মানে করলে দাঁড়ায়: ছায়াশরীরী মদ্যপরিবেশনকারিণী।
ওসব হার্ড-ড্রিঙ্কস্ গেলা আমার ঠিক আসে না। আমি কিলোখানেক কোক নিয়ে, নিলাম। পানির মত ঢকঢক করে হুইস্কি গিলছে একতা। একেবারে খাঁটি, কিচ্ছু মেশায়নি সঙ্গে।
কফস্টার ফার্মহাউসে গাড়ি থামল রাত একটার কিছু পরে। এখানে বিজলিবাতির কোনও কারসাজি নেই। বোঝা যায়, এলাকাটা নিপাট গ্রাম বা বিরান ভূমি। প্রচণ্ড শীতে গাড়ি থেকে নামতে সাহস হচ্ছে না। যদিও আমরা দুজনেই শরীরের আগাপাছতলা সব মুড়ে নিয়েছি ভেড়ার লোমে তৈরি ওভারকোট, মোটা উলেন র্যাপার আর বাঁদুরে টুপিতে। যেন। নতুন কোনও চন্দ্রযানে চেপে চাঁদের বুকে বাড়ি বানাতে যাচ্ছি। আমরা।
এবার হাঁটতে হবে আমাদের। সামনে ওই যে পাহাড় দেখছ, ওটাই বক্সহিল। ওই পাহাড়ের ওপারের ঢালে সেই গ্রেভইয়ার্ড। ওখানেই হয়তো শুয়ে আছেন আমার সার্কাস লেড়ি প্রমাতামহী।
ওঁর নাম কী ছিল? নেহাত বোকার মত প্রশ্ন করি আমি। পরে মনে হলো, এ প্রশ্নের আদতেই কোনও মানে নেই। এক শ বছর আগে যে মরেছে, তার নামে কী এসে যায়!
একতা বলল, ওঁর নাম সিলো সিম্পসন। অ্যাংলো স্প্যানিশ মহিলা, সার্কাসের দলে কাজ করতেন!
রিয়েলি! সার্কাসে কাজ করতেন মানে, নাচতেন বুঝি?
না, নাচাতেন। মায়ের মুখে শুনেছি তিনি সার্কাসের দলে হিংস্র বাঘেদের নাচাতেন। ওঁর কণ্ঠে নাকি জাদু ছিল। তাবৎ পুরুষেরা ওঁর প্রেমে হাবুডুবু খেত। তবে সিলোর জীবনের শেষটা ছিল বড় করুণ।
মানে! কী হয়েছিল ওঁর?
মানে, স্বাভাবিক হয়নি ওঁর মৃত্যুটা। অনেকে অনুমান করেন, যে সার্কাস টিমে তিনি কাজ করতেন, সেই টিমের মালিক আর চিফ ম্যানেজারের লালসার বলি হন সিলো। এদের কেউ একজন দাদিমার মাকে গলা টিপে বা বিষ খাইয়ে হত্যা করে।
সো স্যাড! আমি যুগপৎ দুঃখ ও বিস্ময় প্রকাশ করি। এটা ইংরেজ কেতা। মানতে হয়। হাঁটতে হাঁটতে আমরা প্রায় বক্সহিলের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। শীত এখন আর তত লাগছে না। সয়ে গেছে। বিড়ালের মত সাবধানে পা ফেলে চলতে হচ্ছে, কারণ বক্সহিল এলাকাটা পাথুরে। মাঝে মাঝে অমসৃণ পাথরের চাই মুখ উঁচিয়ে আছে। এর সামান্য ঘষা বা খোঁচা অ্যাডিডাস ব্র্যাণ্ডের কেডস ফুটো করার জন্য যথেষ্ট।
এর পরের ঘটনা বর্ণনাতীত ও ভয়াবহ। বর্ণনাতীত এই কারণে যে, পুরো দৃশ্যপট আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি, আবার মোটা দাগে বলতে গেলে, তা উপলব্ধিরও বাইরে। বক্সহিল গ্রেভইয়ার্ডের পাশে গিয়ে হঠাৎ মনে হলো, আমি এখানে কেন এসেছি! আমার তো কোনও উপলক্ষ নেই! একতাই বা কেন এল! শখানেক বছর আগে ওর প্রমাতামহী সার্কাস দলের নৃশংসতার শিকার হয়েছে, তাতে এত দিন বাদে মাঝরাতে তার কবর জেয়ারতের কী যুক্তি থাকতে পারে!
আসলে মানুষ যখন ভুল করে, যুক্তি-বুদ্ধির ধার ধারে না বলেই তা করে। আমরা এখন বক্সহিল কবরখানার ঠিক দশ গজের ভিতরে অবস্থান করছি। বিশাল এলাকা জুড়ে কবরখানায় শয়ে শয়ে মানুষের কঙ্কাল নিথর শুয়ে আছে। কার কীভাবে মৃত্যু হয়েছে, কে জানে!
আমাকে চমকে দিয়ে চোখের পলকে কবরের কাছে ছুটে গেল একতারিনা। কবরটা একটু ভিতরের দিকে, একতা হাত তুলে ইশারায় ডাকল আমাকে। আকাশে পানসে চাঁদ ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে। আমি আবছা আঁধারে তড়িতাহতের মত চেয়ে দেখছি, পাগলের মত দুহাতে কবরের মাটি খুঁড়ছে একতা। পাশেই উঁচু হয়ে আছে বৃহদাকার ক্রুশ চিহ্ন।
তারপর গলা চড়াল একতা। নীল, এদিকে এসো।
বক্সহিলের চারদিকে পাহাড়ের বেষ্টনীতে বাধা পড়ল। একতার কণ্ঠ। অনুরণিত হলো, নী-ই-ই-ল, এ-স্-স্-সো!
আমি ভয় পাচ্ছি। আমার শরীর ঘামতে শুরু করেছে। কানের ফুটো দিয়ে বেরোল গরম হলকা। ভুল দেখছি?
তারপর মুহূর্ত মাত্র। একতাকে আর দেখা গেল না। সেখানে মাথা তুলল অদ্ভুত এক জিনিস! মুণ্ডহীন কঙ্কাল।
আমি ভুলে গেলাম চোখের পলক ফেলতে। কিংবা ভয়ে। বন্ধ করে ফেলেছি চোখ। একতার দেয়া ছবিতে যাকে দেখেছি, সেই ছায়াশরীর কফিনের পাল্লা খুলে বেরিয়ে এসেছে। একতা পাশে নেই। বা আছে ও নেই-এর মাঝামাঝি কোথাও বিরামহীন দুলছে।
কঙ্কালের দাঁতে তাজা রক্ত। দশ গজ খুব বেশি দূরে নয়, তাই বেশ দেখলাম, একতা তখনও দুলছে হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত রোগীর মত। তারপর?
বিভ্রান্ত হলাম, বুঝলাম না আমার ছুটে পালানো উচিত কি না। তবে আমার বিভ্রান্তি বা অনিশ্চয়তা কেটে গেল খুব তাড়াতাড়ি। কারণ সেই রক্তমুখো ছায়াশরীর ক্রমশ এগিয়ে এল আমার দিকে। আমার বন্ধু একতা নিমিষে ভ্যানিশ! নাকি ডুবে গেল সদ্যখোঁড়া কফিনের ভেতর! ওর প্রমাতামহীর কঙ্কাল বুঝি আর কবরে থাকবে না। মিশে যেতে চাইছে লোকালয়ে, জনারণ্যে। আতঙ্কের ঠাণ্ডা স্রোত নামল আমার শিরদাঁড়া বেয়ে। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। আমি বোধ হয় জ্ঞান হারাচ্ছি।
নিমিষে মনে হলো, চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা। নিতান্ত স্বার্থপরের মত একতাকে ফেলে ছুট দিলাম। অচেনা পথে যেদিকে পারি দৌড়ালাম। বারকয়েক পাথরের চাইয়ে ঠোক্কর খেয়ে পড়লাম মুখ থুবড়ে। তবুও থামলাম না। কারণ, জান বাঁচানো ফরজ।
ভাগ্যিস বিলেতে আসার আগে ড্রাইভিংটা শিখেছি। এবার কাজে লেগে গেল। একতার, বিএমডব্লিউতে চেপে সোজা মোটরওয়ে। তারপর…আর কিছুই মনে নেই।
এ কাহিনীর এখানেই শেষ। তবে কিঞ্চিৎ এপিলগ এখনও বাকি। পরদিন সানডে টাইমস্ লিখল, বক্সহিল গ্রেভইয়ার্ড থেকে কফিন উধাও! এক শ বছর আগের সার্কাস লেডি মিস সিলো সিম্পসনের কফিনে অতর্কিত হামলা। এর পরের খবর সানডে টাইমস জানে না, আমি জানি। আমার প্রিয় বান্ধবী একতারিনাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। যাবে না কখনও। সম্ভবত ছায়াশরীর হাপিস করে দিয়েছে তাকে।
হরর ক্লাব – প্রিন্স আশরাফ
হরর ক্লাবের সদস্য হওয়ার একটাই শর্ত-সদস্যকে ভূতের বলতে হবে। এই শর্ত দেয়ার পরে দেখা গেল-ভূতের গল্প জানা বা বলতে পারা লোকের অভাব নেই। তবে টিভি, ডিশ আর ইন্টারনেটের বদৌলতে মানুষের সময়ের বড়ই অভাব। ক্লাবের সদস্য শুরুতে যতজন ছিল, এখন একুনে দাঁড়িয়েছে এগারোজন। তারমধ্যে প্রতিদিন হাজিরা দেয়ার মত পাঁচজনই নিয়মিত আসে। হরর ক্লাবের সদস্যরা মিলে একটা পোডড়াবাড়ির বেসমেন্টে ক্লাবের পরিবেশ তৈরি করে নিয়েছে। পোডড়াবাড়ির ইলেকট্রিসিটির লাইন কাটা, সেটা আর সংস্কারের চেষ্টা কেউ করেনি। মোমের আলোয় গল্পের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়। অতিরিক্ত কল্পনাবিলাসী ক্লাবের প্রধান উদ্যোক্তা রিটায়ার্ড অফিসার আজমল সাহেব পরিবেশটাকে আরও গাঢ় করতে বিদেশিদের অনুকরণে ফায়ারপ্লেসের ব্যবস্থা করেছেন। মোমের আলোও দূরীভূত হয়েছে। ফায়ারপ্লেসের আগুনের পাশে বসে ওরা চারজন গল্পখখার অপেক্ষা করছে। পাঁচ নম্বর সদস্যের অপেক্ষা। ওরা। জানে, ঝড়, বৃষ্টি, বাদল, বন্যা, ভূমিকম্প যা-ই হোক না কেন। বিমল হালদার আসবেই। একটা ভুতের গল্প না শুনলে বা বললে ওর রাতে ঘুম হয় না। আজ অবশ্য ঝড়, বৃষ্টি, বাদলা কিছুই নেই, শুধু আলকাতরার মত কালো অন্ধকার রাত।
শওকত সাহেব বললেন, নেন, আলতাফ ভাই, একটা কিছু শুরু করেন, রাত বাড়ছে। আজ আর মনে হয় বিমলদা আসবে না।
মুরুব্বি গোছের আলতাফ হোসেন ফায়ারপ্লেসের আগুনের পাশে বসেছিলেন। তিনি ঝিমধরা আগুনটাকে উস্কে দিয়ে বললেন, শীতের রাতে ফায়ারপ্লেসের আগুনের উষ্ণতা কেমন দেখেছেন? গা যেন পুড়ে যায়।
আজমল সাহেব হেসে বললেন, আপনি আগুনের পাশে বসেছেন বলে অমন মনে হচ্ছে, আমার কিন্তু ঠিকই ঠাণ্ডা লাগছে।
শওকত সাহেব একটু সঙ্কুচিত হয়ে বসে বললেন, তাহলে এদিকে সরে এসে বিমলবাবুর জায়গাটাতে বসুন। কি হে, আলতাফ ভাই, ফাঁকি মারতে চাইছেন নাকি? নেন শুরু করুন, আজ আপনার পালা। তবে বিমলবাবু এলে। তাকেই ধরিয়ে দিতাম। ক্লাবের নিয়মানুসারে আমাদের লেট ফি হচ্ছে, গল্প বলাটা লেটকামারের দিকে চলে যাবে।
আলতাফ হোসেন ফায়ারপ্লেস থেকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, আসলে এটা ঠিক গল্প না। অভিজ্ঞতাই বলতে পারেন, তবে আমার না। আমার এক দাদুর। দাদুর মুখেই শুনেছিলাম। সেভাবেই বলছিঃ তখন শরষ্কাল, অপূর্ব হাওয়া। সবাই সন্ধের দিকে নদীর ধারে বেড়াতে যায়। নদীর দুতীর কাশফলে সাদা হয়ে আছে। হাওয়ায় কাশফুল এদিক-ওদিক দুলছে। দাদু দেখলেন, সেই কাশের সাথে আরও একটা সাদা কী যেন দুলছে! সাদা শাড়ির মত…
ঠিক সেই সময়ে দরজায় কাঁচকাঁচ আওয়াজ হলো। হরর ছবির দৃশ্যের মত। শব্দে সবাই চমকে তাকালেন। ফায়ারপ্লেসের আগুন কমে এসেছে। সেই আলোয় সবাই তাকিয়ে আলতাফ সাহেবের বলা গল্পের সাদা শাড়ির মত কিছু একটা দেখতে পেলেন। সাদা শাড়িটা যেন হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে এগিয়ে আসছে। কিন্তু স্বল্প আলোয় তাঁরা শাড়ি আর তার মালিককে চিনতে পারলেন। বিমলবাবু সাদা ফতুয়া আর ধুতি পরে এসেছেন। এই আধুনিক যুগেও ধুতি খড়মের প্রচলন রেখেছেন। আর খড়মের খটখট শব্দেই তারা মুখ না দেখেও বলতে পারেন বিমলবাবু এসেছেন।
আলতাফ হোসেন গল্পের হাত থেকে বাঁচার জন্য গলা চড়ালেন, বিমলদা, নিয়মানুযায়ী আজকের গল্পটা আপনারই পাওনা। আপনি সবার শেষে এসেছেন।
এ বিমলবাবু সোজা গিয়ে ফায়ারপ্লেসের সামনে বসলেন। ফায়ারপ্লেসের দিকে মুখ করে বললেন, ভূতের জন্যই আসতে দেরি হয়ে গেল।
মানে? সবাই সমস্বরে জিজ্ঞেস করলেন।
বিমলবাবু তার উত্তর না দিয়ে কানে গোঁজা পাতার-বিড়ি বের করলেন। তারপর ফায়ারপ্লেসের ভেতর থেকে জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে বিড়ি ধরালেন। বিড়িতে টান দিয়ে শান্তভাবে বললেন, আসার পথে একটা ভূতের সাথে দেখা হয়ে গেল।
ভূতের সাথে দেখা? কোথায়! কীভাবে? আজমল সাহেব জানতে চাইলেন।
এই তো, এখানে আসার পথে। নতুন শ্মশানঘাটের সামনে। দেখলাম জটলা। শ্মশানে দাউদাউ আগুন জ্বলছে। বুঝতে পারলাম কেউ মারা গেছে। একপাশে দাঁড়িয়ে পড়লাম হিন্দু মানুষ। শ্মশান যেন কোন এক আকর্ষণে টানে। যখন চলে আসার জন্য পা বাড়িয়েছি, তখনই তাকে দেখলাম। আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাটা যে ভূত তা বুঝতে পারিনি। তবে পাগল ঠাউরেছিলাম। পাগল না হলে কেউ পুরোপুরি দিগম্বর হয়ে ওভাবে শ্মশানের দিকে তাকিয়ে থাকে।
শওকত হোসেন বললেন, তাই বলুন, ভূত না পাগল! ভূত আবার কেউ দেখে নাকি?
তো প্রথমে পাগলই ভেবেছিলাম। কিন্তু ব্যাটা যখন বিড়ি ধরানোর জন্য ওখান থেকেই দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে শ্মশানের আগুনে বিড়ি ধরাল, তখন আমার ভুল ভাঙল।
আপনি ঠিক দেখেছিলেন? আলতাফ সাহেব জানতে চাইলেন।
এক্কেবারে হানড্রেড পার্সেন্ট ঠিক। কারণ তারপরই আমি তাকে ধরে ফেললাম।
ভূত ধরেছিলেন! সত্যি?
হ্যাঁ। তিন সত্যি। ভাবলাম, জীবনে তো কত ভূতের গল্প করলাম। সেই ভূতই যখন জলজ্যান্ত দেখা দিয়েছে, তখন একে ধরেই ফেলি না কেন?
সবাই একসাথে বলে উঠলেন, ভূত ধরা কি অতই সোজা। তা সেই ভূত এখন কোথায়! কোথায় ধরে রেখেছেন?
আরে আগে ভূত ধরার কাণ্ডটাই শোনেন না।
আজমল সাহেব বললেন, সবাই চুপ করে বিমলবাবুর ভূত ধরার গল্পটা শোনেন। ভূত যখন ধরা আছে, তখন সেটা আমরা স্বচক্ষেই দেখতে পাব, কী বলেন, বিমলবাবু? ভূতটাকে কোথায় আটকে রেখেছেন? গাছের সাথে? আজমল সাহেবের কন্ঠে শ্লেষ ও বিদ্রুপের মিশেল।
বিমলবাবু কোনওদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ফায়ারপ্লেসের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আলো নিভুনিভু হয়ে আসছে। কিন্তু কেউ সেটা বাড়ানোর চিন্তা করছে না। স্বল্প আলোয় বিমলবাবুর মুখ ভালভাবে দেখা যাচ্ছে না। তিনি শান্ত স্বরে বলতে লাগলেন, ভূত বুঝতে পেরে আমি ভাব জমানোর চেষ্টা করলাম। কানে গোঁজা বিড়ি বের করে ভূতের দিকে তাকিয়ে বললাম, দাদা, একটু আগুন হবে?
ভূত ভালমানুষের মত বলে উঠল, কেন দাদা, মুখাগ্নি করবেন?
মুখাগ্নি হিন্দুশাস্ত্রের মরণের পরের বিষয় হলেও বিড়িতে আগুনকে আমরা শয়তানি করে মুখাগ্নিই বলি। কাজেই আমি বিড়ি ধরা মুখটা এগিয়ে দিলাম। আর সেই ভূতটা করল কী, তার মুখটাই এগিয়ে দিল। তবে আমার মত করে না। ঘাড় থেকে ভেঙে মুখমণ্ডল হাতের তালুতে নিয়ে স্বাভাবিকভাবে আমার সামনে বাড়িয়ে দিল। আমি ভেতরে ভেতরে ভয়ে কুঁকড়ে গেলেও, এরকমভাবে বিড়ি ধরালাম যেন ওরকম কন্ধকাটার বাড়িয়ে দেয়া মাথার মুখ থেকে আমি নিয়মিত বিড়ি ধরিয়ে থাকি।
তারপর কী হলো? ভূতটাকে ধরলেন কীভাবে? কাটা মাথা পাকড়ে?
উঁহু। ভূতের সাথে ভাব-ভালবাসা করে। ভূতেরাও ভালবাসায় পটে যায়। ভূতের বিড়ি শেষ হয়ে এসেছে দেখে, আমার কাছ থেকে একটা বিড়ি অফার করলাম। ভূতটা স্বচ্ছন্দে হাত বাড়িয়ে নিল। তারপর মানুষের গলায় বলল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের চিতা জ্বলতে দেখতে দেখতে বিড়িতে সুখটান দেয়ার মত সুখ আর কয়জনের হয়।
আমিও রসিকতা করে বললাম, সবার হয় না, বাপু, আপনার মত দুচারজনের হয়। মরার পরে তো আর সবাই আপনার মত পুণ্যে ভূত হতে পারে না।
ভূতটা হাসল, তা বেড়ে বলেছিস রে, বাছা। কী নাম তোর? তোর সাথে আমার মিলবে খুব। চলে আয় না আমার সাথে, কেউ দেখতেও পাবে না। ধোঁয়ার মধ্যে ওই চিতায় গিয়ে উঠে পড়, তারপর সটান আমার কাছে চলে আয়,
দুজনে মিলে একই বিড়িতে সুখটান দেব।
এখন যেতে পারব না, বাপু। আমার যে একটু কাজ আছে।
মরার চেয়ে কী এমন জরুরি কাজ পড়েছে তোর, বাছা? আমার যদি ক্ষমতা থাকত, তা হলে গলা টিপে মেরে তোর মত বন্ধুকে আমার সঙ্গী করে ফেলতাম। কিন্তু ভূতেরা কাউকে মারতে পারে না, বড়জোর ভয় দেখাতে পারে। তা তুই যে ভয় খাওয়ার লোক নস, সে তো নিজ চোখেই দেখলাম, বাছা। হাতটা বিশ হাত লম্বা করে শ্মশান থেকে আগুন আনলাম। মাথা খুলে দেখালাম, তবু তুই ভয় পেলি না!
মানুষ আর ভূতেরও তো বন্ধুত্ব হতে পারে, বাপু। আমি যখন মরতে পারছি না, তখন আপনি তো আমার সাথ ধরতে পারেন?
মন্দ বলিসনি, বাছা। তা কোথায় যেন চলেছিস তুই?
হরর ক্লাবে। ভূতের গল্পের আড্ডাখানায়। সেখানে সবাই হয় ভূতের গল্প শোনে, না হয় বলে।
কিন্তু কেউ তো আর সরাসরি ভূত দেখতে পায় না, ভূতের মুখ থেকে গল্প শুনতেও পায় না।
না, তা পায় না।
তা হলে আজ আমাকে তোর সাথে করে ওখানে নিয়ে চল। এতদিন শুধু ভূতের গল্প শুনেছে, আজ সত্যিকারের ভূত। দেখুক। ভূতের মুখে গল্প শুনুক।
আপনি যাবেন আমার সাথে?
তুই নিয়ে গেলে যাব। নিয়ে না গেলেও অদৃশ্য হয়ে তোর পিছু নিয়ে চলে আসতে পারি। নিজের চিতা পোড়ানো তো দেখলাম, এখানে আর দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কী? তার চেয়ে তোর সাথে গিয়ে যদি একটু মানুষের সঙ্গ পাই। বেঁচে থাকতে মানুষের একটু সঙ্গ পাওয়ার জন্য খুব হাঁসফাঁস করতাম। তা এই অথর্ব বুড়োর সাথে কে বসে আর বকবক করবে, কার এত সময় আছে? কার এত ঠেকা পড়েছে?
না-না, অদৃশ্য হয়ে যেতে হবে না। আমিই সাথে নিয়ে যাচ্ছি।
তা, তোর ওখানকার অন্যান্য সদস্যরা তোর মতই তো?
মানে? আমার মতই মানুষ কি না? হ্যাঁ, মানুষই। নাকি আপনি তাদের ভূত ভেবেছিলেন?
উঁহু, তা নয়। আমি বোঝাতে চেয়েছি তারাও তোর মত সাহসী মানুষ কি না? ভূতের গল্প বলা ও শোনা এক জিনিস আর সরাসরি ভূত দেখা অন্য জিনিস। বয়স্ক মানুষ হলে ভয়ে গোঁ-গোঁ করে অজ্ঞান হয়ে পড়তে পারে। শেষে যমে-মানুষে আর ভূতে মিলে টানাটানি শুরু হবে। তার চেয়ে না হয় তোর সাথে অদৃশ্য হয়ে…
তা মন্দ বলেননি, ওখানে সবাই আমার মত ঠিক সাহসী নয়। সুদখোর আজমইল্যা তো টাকার গরমে অজ্ঞান হয়ে থাকে। টাকার গরমেই পোড়োবাড়ি কিনে ভূতের। আড্ডাখানা বসিয়েছে। আর বুড়োভাম আলতাফ খুড়ো তো নিজেকে সর্বজ্ঞানী ভাবে, ওদিকে ওর আত্মীয়স্বজনরা যে সব ফাঁকা করে দিচ্ছে সে খেয়াল বুড়োভামের নেই। শওকত। চোরা নিজেরে সাহসের ডিপো ভাবলেও ওটা এক্কেবারে ভিতুর ডিম। আপনাকে দেখে এক্কেবারে কাপড় খারাপ করে ফেলবে।
আজমল সাহেব, আলতাফ সাহেব আর শওকত হোসেন তিনজনই সমস্বরে বলে উঠলেন, এসব কী বলছেন, বিমলবাবু? আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? ভূতের চক্করে পড়ে? আমাদের সম্বন্ধে কী সব আজেবাজে কথা বলছেন!
সর্বকনিষ্ঠ ও সবচেয়ে চুপচাপ সদস্য জসিম মণ্ডল বলল, বিমলদা, ফায়ারপ্লেসের আগুনটা একটু উস্কে দেন না, কেমন
অন্ধকার হয়ে এসেছে।
বিমলবাবু শান্ত মুখে বললেন, ফায়ারপ্লেসের ভেতরে তেমন কিছু নেই, উস্কে দিলেও লাভ হবে না। নতুন কাঠ দিতে হবে। শওকত চোরারে কাঠ চুরি করে আনতে বলো।
শওকত হোসেন ক্ষুব্ধ স্বরে বললেন, ভাল হচ্ছে না কিন্তু, বিমলদা। বয়োজ্যেষ্ঠ বলে আপনাকে কিন্তু যথেষ্ট সম্মান করি, তাই বলে মুখে যা আসে আবোলতাবোল বলে যাবেন! শওকত হোসেন রেগেমেগে উঠে দাঁড়ালেন।
শওকত হোসেনের দেখাদেখি আলতাফ সাহেব ও আজমল সাহেবও উঠে দাঁড়ালেন। ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে এগিয়ে এলেন বিমলবাবুর দিকে। ইচ্ছে-কলার ধরে দুটো ঝাঁকুনি দিয়ে এসব কথার ব্যাখ্যা চাইবেন।
ফায়ারপ্লেসের কাছটাতে অন্ধকার। আগুন প্রায় নিভু নিভু। কাঠপোড়া কয়লার নিচে গনগনে লালচে আভা দেখা যাচ্ছে।
জসিম মণ্ডল উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কাঠ আনা নিয়ে ঝগড়া করে লাভ নেই, শওকত ভাই। আমিই কাঠ নিয়ে আসছি।
বিমলবাবু শান্ত স্বরে বললেন, আপনাদের কাউকেই উঠতে হবে না, জায়গায় বসুন। কাঠের ব্যবস্থা আমিই করছি।
শওকত হোসেন খেপে গেছেন। তিনি চিবিয়ে-চিবিয়ে বললেন, তোর কাঠের খ্যাতা পুড়ি আমি। তুই আমারে চোর বলেছিস, বিমল। তোরে আজকে ওই ফায়ারপ্লেসের আগুনে পোড়াব। হিন্দু মানুষ, পুড়েই তো তোদের শান্তি, কাঠকয়লা পোড়া হয়ে ভূত হয়ে যাবি তুই।
তার আর দরকার হবে না, শওকত চোরা। তোদের সুবিধা করে দিচ্ছি।
শওকত হোসেন বিমলবাবুর কথা ধরতে পারলেন না। গলার টুঁটি টিপে ধরার জন্য এক লাফে ফায়ারপ্লেসের কাছে বিমলবাবুর মুখোমুখি হলেন।
তারপর অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলেন…
ফায়ারপ্লেসের আগুন বেড়ে যাচ্ছে! নতুন কাঠ দিলে যেমন উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে ওঠে, তেমনটি। আর সেই আগুন বেড়ে ওঠার কারণ বিমলবাবু তার ডান হাতের কনুই পর্যন্ত ফায়ারপ্লেসের জ্বলন্ত কাঠকয়লার মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছেন।
আগুনে পোড়াতে এসে বিমলবাবুর হাত আগুনের মধ্যে দেখে আঁতকে উঠলেন শওকত হোসেন। বিমলবাবুর হাতটা ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে বললেন, এ কী পাগলামি করছেন, বিমলবাবু? এমন কাজ কেউ করে?
হাতটা টেনে বের করে হতভম্ব হয়ে গেলেন শওকত হোসেন। হাতের আঙুল থেকে কনুই পর্যন্ত দাউ দাউ করে জ্বলছে। ততক্ষণে বাকি তিনজনেও কাছে এসে পড়েছে।
হাতের দাউদাউ আগুনে সবাই বিমলবাবুর মুখ দেখতে পেল এবার। সে মুখ যে বিমলবাবুর, তা কেউ বলতে পারবে না। আগুনে পুড়ে ঝলসানো, বিকৃত, বীভৎস একটা মুখের আদল…।
ভয় পেলে যে মানুষের অবস্থা কেমনতরো হয়, তা এই বয়স্ক মানুষগুলোকে দেখলে বোঝা যেত। তারা সবকিছু ফেলে ভেঙেচুরে এমনভাবে দৌড় শুরু করলেন, যেন অলিম্পিকের প্রবীণ সোনাজয়ী দল।
বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে তারা শোনের কাছে এসে পড়লেন। বাড়ির পথেই শুশানটা পড়ে। শ্মশানে তখন মড়া পোড়ানোর দল শেষ ছাইটুকু রেখে চলে আসার তোড়জোড় করছে।
ওরকম হন্তদন্ত হয়ে তিনচারজন বয়স্ক মানুষকে ছুটে আসতে দেখে তারা অবাক হলো। একজন প্রবীণ মানুষ প্রায় পথ আগলেই জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে, আজমল ভাই, অমন করে দৌড়াচ্ছেন কেন?
আজমল হোসেন হাঁপাতে হাঁপাতে কোনওমতে বললেন, বিমলবাবু…
প্রবীণ বুঝদারের মত মাথা নেড়ে বললেন, হু, বিমলবাবু আজ সন্ধেয় মারা গেছেন। তার খবর আপনারা এখন পেয়েছেন? তাই এভাবে ছুটতে ছুটতে আসছেন?
প্রবীণের কথাতে ওরা থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কোনওমতে ঢোক গিলে তো-তো করে বলতে পারল, বিমলবাবু মারা গেছেন!
হু। আজ সন্ধেয়, ছাদের কার্নিশ থেকে পড়ে। থেঁতলে বীভৎস চেহারা হয়ে গিয়েছিল। এই তো, আমরা বিমলের মড়া পুড়িয়ে চান করতে যাচ্ছি। তা যান না শ্মশানের কাছে। বন্ধুকে শেষ দেখাটা দেখে আসেন। এখন অবশ্য একমুঠো ছাই ছাড়া কিছুই দেখতে পাবেন না। সবাই ছাই হয়ে যায়…ছাই…
জটা পাগল ও জিনের বাদশা – রাকিব হাসান
বর্ষাকাল। সুতরাং বৃষ্টি তো হবেই। তবে এবারের বৃষ্টির পরিমাণটা একটু বেশি। গত চারদিন ধরে একটানা বৃষ্টি হচ্ছে। আকাশের যেন কোনও ক্লান্তি নেই। নেই কোনও অবসর কিংবা বিরক্তি। এক সেকেণ্ডের জন্যও বৃষ্টি থামেনি। কখনও টিপটিপু, কখনও মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। শহুরে জীবনযাপন বাধাগ্রস্ত হলেও গ্রাম্য জীবনযাপনে এরকম বৃষ্টির প্রভাব বেশি। চুলোয় রান্না-বান্না; হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল পালন সবক্ষেত্রেই বাধার সৃষ্টি হয়।
এরকম বৃষ্টির এক রাতে সেলিম রেল স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। রেল স্টেশন থেকে তার বাড়ি চার কিলোমিটার দূরে। কাঁচা রাস্তা বলেই ঝামেলা বেশি। বর্ষাকালে এই রাস্তায় ভ্যানগাড়ির বদলে গরুর গাড়ি চলে। সুতরাং রাস্তা এবড়োখেবড়ো-কাদামাখা। এই বৃষ্টিতে গরুর গাড়ি তো দূরে থাক একটা শিয়াল-কুকুরও রাস্তায় আছে কিনা সন্দেহ।
সেলিমের মনটা আনচান করে। তার বাড়ি ফেরা খুবই প্রয়োজন। বিকালের মধ্যেই ট্রেন এখানে পৌঁছে যাবার কথা থাকলেও আসতে পারেনি। এই স্টেশনে এসেছে রাত দশটায়। তখন বর্ষার আকাশ-বাতাস কাঁপানো বর্ষণ ছিল। সেলিম বৃষ্টি কমার অপেক্ষা করতে করতে দুঘণ্টা পার হয়ে গেলেও বৃষ্টি তো কমেইনি তার উপর ঝড় আরম্ভ হয়েছে। এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে চার কিলোমিটার কাদামাখা পথ পাড়ি দেয়া চাট্টিখানি কথা নয়।
তবে মনের কাছে কোনও সমস্যাই সমস্যা নয়। ইচ্ছা কখনও যুক্তি তর্ক মানে না। মানে না কোনও সমস্যা। সেলিমের মন পড়ে আছে বাড়িতে। কারণ বাড়িতে তার সুন্দরী নববধূ তার পথ চেয়ে আছে। সেলিম নরসিংদী শহরে কাপড়ের ব্যবসা করে। মাঝে মাঝে রাতে বাড়ি ফেরে না। তার বউ মরিয়ম তার পথ চেয়ে নিঘুম রাত পার করে দেয়।
আজ চারদিন পর সেলিম বাড়ি ফিরছে। বিয়ের পর সে কখনও চাররাত বাড়ির বাইরে থাকেনি। তার বিয়ে হয়েছে মাত্র তিন মাস। সদ্য বিয়ে করা নববধূকে ফেলে চাররাত বাইরে থাকতে বেশ কষ্ট হয়েছে সেলিমের। কিন্তু কোনও উপায় ছিল না। তাই আজ এই ঝড়বৃষ্টি মাথায় নিয়ে অনেকখানি পথ পাড়ি দিয়ে সেলিম ভালবাসার টানে তার বউয়ের কাছে এসেছে।
ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই রাস্তায় নেমে পড়ে সেলিম। প্যান্ট গুটিয়ে হাঁটুর উপরে এনেছে। পায়ের স্যাণ্ডেল এখন তার হাতে। প্রায় কচ্ছপগতিতে তাকে এগোতে হচ্ছে। রাস্তায় পা ফেলার সাথে সাথেই হাঁটু অবধি কাদার মধ্যে ডুবে যাচ্ছে। শক্তি প্রয়োগ করে পা উঠিয়ে অন্যখানে ফেললেও সেই একই অবস্থা। মনে মনে মরিয়মের কথা ভাবতে ভাবতে এগোতে থাকে সে।
মরিয়ম দেখতে খুবই সুন্দরী। একেবারে পরীর মতন। দুধে আলতায় গায়ের রঙ, মায়াবী মুখের চেহারা, টানা টানা চোখ, বাঁশির মত নাক-সবমিলিয়ে অপূর্ব সুন্দরী। গ্রামে এমন মেয়ে বিশেষ পাওয়া যায় না। সেলিমদের বাড়ির কয়েক গ্রাম পরেই মরিয়মের বাপের বাড়ি। মরিয়ম সুন্দরী হলেও কোনও ছেলে তার ধারে কাছে ঘেঁষত না। সবাই বলে জিনের বাদশা নাকি মরিয়মের রূপে পাগল। মরিয়মের দিকে কোনও ছেলে হাত বাড়ালে তার ক্ষতি হবে। কোনও ছেলেই তাই মরিয়মকে কাছে পাবার চেষ্টা করে না। বিয়ের জন্য সম্বন্ধ এলে তা ভেঙে যায়। কোনও বাবা-মা চায় না সুন্দরী বউ পাওয়ার জন্য নিজের ছেলের ক্ষতি করতে।
মরিয়মের কৃষক বাবার দুঃখ কম ছিল না। সুন্দরী মেয়ে ঘরে অবিবাহিতা থাকলে বাবারা রাতে ঘুমাতে পারে না। সুন্দরী আবার ভয়ঙ্করও। মাঝে মাঝে মধ্যরাতে মরিয়মের ঘর আলোয় ভরে ওঠে। কড়া মিষ্টি আতরের গন্ধ পাওয়া যায়। তাই সে তার মেয়েকে কখনও বকাঝকা করে না। বরং মেয়েকে ভয় পায়।
সেলিমের কথা একটু আলাদা। মা-বাবা-ভাই-বোন কেউ নেই তার। আপন বলতে এক চাচা আছে। সেই চাচাই সেলিমকে মরিয়মের কথা বলেছে। একদিন চাচার সাথেই মরিয়মকে দেখতে যায়। মরিয়মের রূপে সেলিম আত্মহারা। রূপবতী এই মেয়েকে তার বউ হিসাবে চায়। মরিয়মের বাবা সব কথা খুলে বলে।
সেলিম নিজের জীবনের উপর ঝুঁকি নিতে রাজি মরিয়মকে পাবার জন্য। সেলিমের চাচা ভাতিজার এ ইচ্ছা মেনে নিতে চায় না। কিন্তু সেলিমের পীড়াপীড়িতেই রাজি হয়। তবে তার আগে জটা পাগল নামে তান্ত্রিকের কাছ থেকে সেলিমের কাছে থাকবে ততক্ষণ কোনও জিন তার ক্ষতি করতে পারবে না। তাবিজটি সবসময় সেলিমের ডান বাহুতে বাঁধা থাকে।
বাড়ির কাছাকাছি আসতেই সেলিমের গা ছমছম করে। এখন তাকে কবরস্থানের পাশ দিয়ে যেতে হবে। এই কবরস্থান সম্বন্ধে নানান গালগল্প আছে। আগেও রাতে অনেকবার এই কবরস্থানের পাশ দিয়ে সেলিম বাড়ি ফিরেছে, কিন্তু আজকের অবস্থা অন্যরকম।
.
ঘুটঘুঁটে অন্ধকার রাত, তার উপর আবার ঝড়-বৃষ্টি। অন্ধকারে একবার ভুল পথে পা বাড়িয়েছিল। কিছুদূর যাবার পর বিজলীর আলোয় সে বুঝতে পারে পথ ভুল হয়েছে।
মনে মনে দোয়া পড়তে পড়তে পা বাড়ায় সেলিম। এই অল্প পথ যেন শেষ হতে চায় না। সামান্য শব্দেই গা কেঁপে ওঠে। মনে হয় কে যেন তার পিছু পিছু হটছে। ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকিয়ে দেখার মত সাহস তার হয় না।
অবশেষে সে কবরস্থান পার হয়ে আসে। এই বৃষ্টির মধ্যে তার গা ঘেমে গেছে। মনে হচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেগেছে। কবরস্থান পার হয়ে আসতে।
একসময় সে বাড়ির কাছে চলে আসে। সে বুঝতে পারে মধ্যরাত পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ আগে। তবুও সে তার মরিয়মের কাছে আসতে পেরেছে এটাই বড় কথা। ভালবাসার টান কিংবা কাছে পাবার টান কখনও কোণও বাধা মানে না। সেলিম তার ঘরের বারান্দায় উঠে গা ঝাড়তে থাকে। মরিয়ম নিশ্চয়ই তাকে দেখে অবাক হবে। খুশি তো হবেই! এসময় সেলিমের নাকে তীব্র ফুলের গন্ধ প্রবেশ করে। কিন্তু তার বাড়িতে তো কোন ফুলের গাছ নেই! তা হলে ফুলের মিষ্টি গন্ধ কোথা হতে আসছে! চমকায় সেলিম। দরজায় টোকা দিতেই সে খেয়াল করে নিচ দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। তার মানে মরিয়ম জেগে আছে। কিন্তু এত রাতে তো জেগে থাকার কথা নয়!
মনের মধ্যে সন্দেহ ঢুকে পড়ে সেলিমের। মরিয়ম কি পরপুরুষের সাথে…ছিঃ। মরিয়ম এমনটা করতে পারে না! কিছুতেই পারে না। চঞ্চল চোখজোড়া ঘরের ভিতরের দৃশ্য দেখতে চায়। একটা ছোট্ট ফুটো যেন তার খুব প্রয়োজন। মা মনসাও হয়তো লখিন্দরের লোহার বাসরে ফুটো খোঁজার জন্য এত অস্থির হয়নি।
সেলিম বিশ্ব জয় করার আনন্দ পায় জানালার নিচে একটা ছোট ফুটো খুঁজে পাওয়ায়। দেরি না করে চোখ লাগায় তাতে। চমকে ওঠে সে। বিশ্বাস হতে চায় না! অবিশ্বাস্য! মরিয়ম গভীর ঘুমে মগ্ন। তাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে আছে সুদর্শন এক যুবক। যুবকের শরীর হতে আলো ছড়াচ্ছে। সেই আলোয় ঘরের অন্ধকার দূর হয়ে গেছে।
অসঙ্গতিটা ধরতে পারে না সেলিম। তীব্র রাগ, ক্ষোভ, ঘৃণা এসে ভর করে। চিঞ্জার করে দরজায় থাবা দেয়। খানকি মাগী, দরজা খোল…দরজা খোল্ কইলাম…ওরে, মাগী…বেশ্যা… সেলিম দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে দরজায় আঘাত করতে থাকে। তার মুখ থেকে ছোটে অশ্লীল সব শব্দ। ঘুম জড়ানো চোখে দরজা খোলে মরিয়ম। দমকা হাওয়ার মত ঘরে ঢোকে সেলিম। অনবরত মরিয়মকে মারতে থাকে। মরিয়ম ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। বিস্ময়ের জন্য হয়তো __ লাগে না। মরিয়ম মাটিতে পড়ে যেতেই রাগটা যুবকের উপর গিয়ে পড়ে। কিন্তু কোথায় সেই যুবক! নেই! যেন শূন্যে মিলিয়ে গেছে। তা হলে কি চোখের ভুল!
এবার সেলিমের বিস্মিত হবার পালা। অসঙ্গতিটা বুঝতে পারে। যুবকের গা হতে আলো বেরুচ্ছিল কেন? তা হলে কি যুবকটি মানুষ নয়! জিনের বাদশা! মূর্তির মত দাঁড়িয়ে থাকে। সে। শ্বাস নিতেও যেন ভুলে গেছে।
মরিয়ম উঠে বসে। সে-ও অবাক হয়েছে। তার স্বামী এই মাত্র বাড়ি ফিরল, তা হলে স্বামীর ছদ্মবেশে তিনরাত তার সাথে থাকল কে? তা হলে কি সে অন্য কেউ? গভীর রাতে তার স্বামীর রূপ ধরে আসে আবার ভোর হবার আগেই চলে যায়! প্রথমরাতে স্বামীর ছদ্মবেশীর আদর-সোহাগ দেখে অবাক হয়েছিল।
স্বামীর পা ধরে কাঁদতে কাঁদতে সব খুলে বলে মরিয়ম। কোনও কিছুই গোপন করে না। সব শুনে সেলিম ভয় পায়। নির্দোষ স্ত্রীকে বেদম মারধর করায় অপরাধবোধ জন্ম নেয়।
সে রাতে আর তাদের ঘুম হয় না। একটু পরেই মসজিদ থেকে সুরেলা আজানের ধ্বনি ভেসে আসে। দুজনেই ভয় নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে দিনের আলোর জন্য। সূর্য ওঠার সাথে সাথেই জটা পাগলের কাছে রওনা হয় সেলিম। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাকে নিয়ে হাজির হয়। সব শুনে ও বুঝে বিজ্ঞের মত মাথা দোলায় জটা পাগল।
বিপদ…বিপদ আইতাছে…ঘোর বিপদ সামনে…জিনের বাদশা…খুবই শক্তিশালী। থেমে থেমে শীতল কণ্ঠে চিৎকার করে জটা পাগল। তার কণ্ঠে এমন কিছু ছিল যা সেলিমের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেয়। সেলিম জটা পাগলের পা ধরে কেঁদে ফেলে।
পাগল বাবা, আমাগোরে বাঁচান…যেমনেই হোক আমাগোরে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। হাউমাউ করে কাঁদতে থাকে সেলিম।
সন্ধ্যার পর আমি আইতাছি। তোর বউয়ের কাছ থেইক্যা জিনের বাদশারে খেদাইতে হইব। গম্ভীর কণ্ঠে বলে জটা পাগল।
দুজনের সন্ধ্যা হবার অপেক্ষা। শত ঝামেলার মধ্যেই ক্ষুধার্ত স্বামীর জন্য রান্না করে মরিয়ম। সেলিম কিচ্ছু খেতে পারে না। মরিয়মের সাথে কথাও বলে না। হয়তো নিজের। স্ত্রীর পাশে অন্য কাউকে দেখতে চায় না। সে জিন হোক বা মানুষ।
সন্ধ্যার কিছুক্ষণ আগে জটা পাগল সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন। করে সেলিমের বাড়িতে চলে আসে। বাড়ির চারদিকে বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে। বিড়বিড় করে কী যেন বলে। সন্ধ্যার পর উঠানে একটা হাড় দিয়ে বৃত্ত আঁকে মাটির বুকে। বৃত্তের ভিতরে প্রবেশ করে সেলিম, মরিয়ম এবং জটা পাগল। বৃত্তের চারদিকে জ্বলে মোমবাতি।
গ্রামের সমস্ত মানুষ বৃত্তের বাইরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে যায়। কেউ কেউ দূর থেকে দেখতে থাকে। সেলিমের বাড়িতে মানুষের অভাব হয় না। তারা সবাই জটা পাগলের ক্ষমতা দেখতে উৎসুক।
আস্তে আস্তে রাত বাড়তে থাকে। মানুষের উৎসাহে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়ে না। বরং আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। সেই সাথে বাড়তে থাকে জটা পাগলের মন্ত্র পড়ার শব্দ। একসময় দমকা বাতাস বয়ে যায়। লোকে ভাবে এ বুঝি জিনের বাদশার আগমনী বার্তা।
এত লোকের ভিড়েও কোনও শব্দ হয় না। শুধু মন্ত্র পড়ার শব্দ। হঠাৎ কোথা থেকে যেন হাসির শব্দ ভেসে আসে। লোকজন একে অপরের গায়ের সাথে সেঁটে যায়। তারা যেন শ্বাস নিতে ভুলে গেছে।
হঠাৎ কোথা থেকে যেন ভারী বজ্রপাতের মত শব্দ ভেসে আসে।
আমাকে বিরক্ত করার সাহস পেলি কোথা থেকে? অদৃশ্য কেউ একজন বলে ওঠে।
মরিয়মরে ছাইড়া দে। না দিলে তোর ক্ষতি হইব। মন্ত্র পড়া বাদ দিয়ে চিৎকার করে জটা পাগল।
তোর এত্ত বড় সাহস আমার ক্ষতি করবি। আমি জিনের বাদশা, আমি সব পারি। আজকেই মরিয়মকে নিয়ে যাব আমি। তোর ক্ষমতা থাকলে আটকা। হেসে ওঠে অদৃশ্য কণ্ঠধারী।
তাইলে তই আমার কথা শুনবি না? দেখ আমি কী করি। চিৎকার করে জটা পাগল। হাতের মুঠো থেকে কী যেন বের করে আগুনে ফেলে দেয়। চিৎকার করে ওঠে অদৃশ্য কণ্ঠধারী। ধোয়ায় ভরে যায় চারপাশ। কেউ কাউকে দেখতে পায় না। ধোয়া সরে যেতেই হঠাৎ সব আলো নিভে যায়। চাঁদখানাও ডুব দেয় মেঘের আড়ালে। কৌতূহলী দর্শকদের মনে ভয় ঢুকে যায়। অন্ধকারে ডুবে যায় সমস্ত গ্রাম। কেউ কিছু দেখতে পায় না। শুধু ধস্তাধস্তির শব্দ ভেসে আসে।
একসময় মেঘের আড়াল থেকে চাঁদ বের হয়ে আসে। চাঁদের আলোয় লোকজন স্পষ্ট দেখতে পায় বৃত্তের ভিতর সেলিম এবং জটা পাগলের নিথর দেহ পড়ে আছে। মরিয়মকে কোথাও দেখা যায় না। যেন এত লোকের মধ্য হতে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে।
শিকার – মিজানুর রহমান কল্লোল
উন্মাদ পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক সাজ্জাদ কবিরের সাথে আমার দীর্ঘদিন দেখা হয় না। এক সময় প্রতিদিন দেখা হত। আমি হাসপাতালের ডিউটি সেরে দুপুরে আরামবাগে তাঁর অফিসে যেতাম। প্রায় ঘণ্টাদুয়েক আড্ডা দিতাম। দুনিয়ার হাবিজাবি বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। সেই সঙ্গে মুখে চলত একটু পরপর চা, সিগারেট আর চানাচুর। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লেখক মোকারম হোসেন তখন শিশু একাডেমিতে চাকরি করত। সে একফাঁকে এসে যোগ দিত আমাদের সাথে। তিনজনের আড্ডার মধ্যে উন্মাদ অফিস থেকে সম্পাদক আহসান হাবীব ফোন করে বলতেন, খুব জরুরি, এখনই সবাইকে উন্মাদ অফিসে যেতে হবে। আমি ও মোকারম সাজ্জাদ কবিরের মোটর সাইকেলের পেছনে চেপে বসতাম। একটানে ধানমণ্ডির অফিসে চলে যেতাম। গিয়ে দেখতাম হাসান খুরশীদ রুমী যথারীতি নানরুটি আর কাবাব নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমরা খাবারের ওপর হামলে পড়তাম। এরপর আবার আড়া। আবার চা, সিগারেট আর চানাচুর। এভাবেই চলছিল দিন। এরপর হঠাৎ একদিন আমরা প্রাত্যহিক রুটিন পরিবর্তন করে ফেলি। আমি বিকালে পুরান ঢাকার একটি চেম্বারে বসা শুরু করলাম। হাসান খুরশীদ রুমী তাঁদের বাড়ির কাজ শুরু করার অজুহাতে উন্মাদে আসা বাদ দিলেন। মোকারম প্রতি মাসে একটি করে বই লিখতে লাগল। আর সাজ্জাদ কবির ভাই একটি নোটিশ টানিয়ে তাঁর অফিসটাকে আড়ামুক্ত এলাকা ঘোষণা করলেন। উন্মাদ অফিসটাও ধানমণ্ডি এলাকা থেকে চলে গেল মিরপুরে। আমাদের কোথাও আড্ডা বলতে আর কিছুই থাকল না। তাই একদিন সাজ্জাদ কবির ভাই যখন ফোন করে তার অফিসে কফি খাওয়ার দাওয়াত দিলেন এবং বললেন যে কফি খেয়েই একসাথে উন্মাদ অফিসে যাওয়া হবে, আমি আর দেরি করতে পারলাম না। ন্যাশনাল হাসপাতাল থেকে বেরিয়েই একটা রিকশা নিয়ে ছুটলাম আরামবাগ। রিকশায় বসে মোকারমকে ফোন করলাম। কিন্তু তার মোবাইল বন্ধ পেলাম। যতবার ফোন করি ততবার এক মহিলার বিরক্তিকর কণ্ঠ-দুঃখিত, আপনার কাঙ্ক্ষিত নম্বরটি এই মুহূর্তে বন্ধ রয়েছে…
রিকশাওয়ালাকে অতিরিক্ত দশ টাকা বকশিশ দিয়ে আরামবাগে দেওয়ানবাগ হুজুরের বাবে রহমতের গলির সামনে নেমে পড়লাম। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দ্রুত ঢুকে পড়লাম গলিতে। এই গলির শেষমাথায় সাজ্জাদ ভাইয়ের সৃতি প্রেস।
অনেকে বিভিন্ন সময়ে জানতে চেয়েছে স্মৃতি না হয়ে সৃতি কেন? সাজ্জাদ ভাই উত্তরে বলেছেন, আমার ইচ্ছা। কিন্তু পরে শুনেছি সৃতি হলো গতিময় পথ।
নিজের প্রেসের ভেতরে সুন্দর করে সাজানো ছোটখাট একটা অফিস। কাঁচের টেবিলের ওপাশটায় তিনি বসে থাকেন। এপাশে তিনটে চেয়ার আর দুটো সোফা। পাশে ছোট্ট একটা রুম। ওখানে বসে তাঁর ছোট ভাই আসরার মাসুদ প্রগতি পাবলিশার্সের কাজ করে। সব মুখস্থ আমার।
কিন্তু এখন গিয়ে দেখি অফিসটা ওখানে নেই! নেই প্রেসের কোন চিহ্ন!
১৪৫/৩ নম্বরটিই আমি খুঁজে পেলাম না।
একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, সৃতি প্রেসটা কই?
সে বলল, ওটা তো এক বছর আগেই এখান থেকে চলে গেছে।
কোথায় গেছে?
জানি না।
জানেন না মানে? ঘটনাবহুল প্রেস!
লোকটা সরু চোখে আমার দিকে তাকাল। ঘটনাবহুল? কীসের ঘটনাবহুল?
আমি উত্তর না দিয়ে সামনে এগোলাম। পকেট থেকে মোবাইল বের করে কল দিলাম সাজ্জাদ ভাইয়ের নম্বরে। নম্বরটি বন্ধ।
আবার কল দিলাম। বন্ধ।
আবার–আবার-বারবার—
বন্ধ। বন্ধ।
মেজাজ খারাপ হতে লাগল।
কোন মানে হয়?
সাজ্জাদ ভাই তার প্রেস এখান থেকে সরিয়ে নিয়েছেন সেটা আমাকে জানাবেন না? ওদিকে তিনি মোবাইলও বন্ধ রেখেছেন।
জুলাইয়ের তীব্র গরম। মাথার ওপর গনগন করছে সূর্য। এক ফোঁটা বাতাস নেই কোথাও। কোন গাছের পাতাই নড়ছে না। ঘেমে শরীরের সাথে লেপ্টে আছে শার্ট।
একটা চায়ের দোকানের সামনে লোকজন ভিড় করে চা খাচ্ছে। এই গরমে সবাইকে এভাবে চা খেতে দেখে আরও গরম লাগল আমার। সেই সাথে মেজাজও চড়তে থাকল।
হঠাৎ সেই ভিড়ের ভেতর থেকে একজন যুবক বেরিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমার কাঁধে টোকা দিয়ে বলল, এই, তুই রাজেশ না?
আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি রাজেশ। কিন্তু তুই কে? আমাকে তুই করে বলাতে আমিও ইচ্ছা করেই তাকে তুই করে বললাম।
আমি এমনই।
যে আমাকে যা দেয়, আমি সেটাই তাকে ফিরিয়ে দিই। আমাকে আপনি করে বললে আমিও তাকে সম্মান করে আপনি সম্বোধন করি। আমাকে তুমি করে বললে আমিও। বিগলিত হয়ে তুমি বলি। আর কেউ তুই বললে তাকেও তুই। এর যেমন ভাল দিক আছে, খারাপ দিকও আছে। একবার মতিঝিল এজিবি কলোনির এক বাসার পেছনে দাঁড়িয়ে দেয়ালে প্রস্রাব করছিলাম, হঠাৎ শুনি পেছনে কেউ বলছে, এই, ছেলে, কী করিস এখানে?
আমি মাথা না ঘুরিয়েই বললাম, কানা নাকি? দেখস না কী করি? আয়। লাইনে দাঁড়া।
কী? কী বললি, বদমাশ ছেলে?
তাকিয়ে দেখি মুনিয়ার বাবা।
আমি প্যান্টের চেইন না আটকিয়েই ঝেড়ে দৌড় দিলাম। মুনিয়ার সাথে আমার বিয়ের কথাবার্তা চলছিল।
এরপর ওখানেই পরিসমাপ্তি।
মুনিয়া স্রেফ আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল, কোন কুকুর স্বভাবের লোকের সাথে বাবা আমাকে বিয়ে দেবেন না।
আমি আর কথা বলারই সুযোগ পাইনি।
যুবক আবার টোকা দিল আমার কাঁধে।
আমি ঠিকই চিনেছি। তুই রাজেশ। তোকে রাজ বলে ডাকতাম। কতদিন পর দেখা।
আমি এক পা পিছিয়ে গিয়ে বললাম, কিন্তু তুই কে?
আমাকে চিনিস নাই? আমি অভিজিৎ।
অভিজিৎ? আমি ঠিক চিনতে পারলাম না তাকে।
হ্যাঁ, অভিজিৎ।
সে হাসল। আমি স্মৃতি হাতড়ালাম।
বরিশাল মেডিকেলে আমার সাথে অভিজিৎ নামে কেউ পড়ত না। আমাদের আগের ব্যাচে এক অভিজিন্দা ছিলেন, কিন্তু এর সাথে তার চেহারার মিল নেই।
আমার চেহারা বোধহয় পড়তে পারল সে। একটু হেসে বলল, নন্দিতাকে ভুলে গেছিস তুই? অবশ্য ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক। সে তো আজকের কথা নয়!
বিদ্যুৎ চমকের মত আমার মনে পড়ে গেল। আমি চিৎকার করে তাকে জড়িয়ে ধরতে গেলাম। সে পেছনে সরে গেল।
আমি একটু ধাতস্থ হয়ে বললাম, নন্দিতা কেমন আছে রে?
সে বলল, খুব ভাল আছে। কাল ওর বিয়ে। নন্দিতাকে কথা দিয়েছিলাম ওর বিয়েতে তোকে হাজির করব। যে কষ্ট ওকে দিয়েছিলি, মেয়েরা সহজে কষ্টের কথা ভোলে না।
আমি একটু থমকে গেলাম। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বললাম, অভিজিৎ, ওটা ছিল একটা অ্যাকসিডেন্ট।
এতদিন পর আমি ব্যাখ্যা শুনতে আসিনি। নন্দিতাকে কথা দিয়েছিলাম, ব্যস, আমি কথা রক্ষা করছি। তোর হাসপাতালেই যেতাম। কিন্তু তোর সাথে এখানেই দেখা হয়ে গেল।
তুই জানিস আমি কোন্ হাসপাতালে?
না জানার কী আছে? তুই এত বিখ্যাত হয়ে গেছিস!
আমি অভিজিৎকে দেখছি। একসাথে স্কুলে পড়তাম আমরা। খুব ছটফটে ছিল সে। ভাল ফুটবল খেলত। ম্যাট্রিক পাশ করার পর সে হঠাৎ করে সায়েন্স ছেড়ে আর্টস নেয়। তাই তার সাথে আমার আর দেখা হত না।
কিন্তু আমার সাথে দেখা হত নন্দিতার। প্রায় নিয়মিত। আমি তখন ইন্টারমিডিয়েট সেকেণ্ড ইয়ারে।
একদিন ক্লাস ছিল না। আমি কলেজের পেছনের খেজুর বাগানে একটি খেজুর গাছের গোড়ায় বসে ছবি আঁকছিলাম। হঠাৎ মেয়ে কণ্ঠের হাসি শুনে চমকে তাকাই। তেরো-চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে। অদ্ভুত সুন্দরী।
কার ছবি আঁকছেন?
অ্যাঁ! কারও না। এমনি এক মেয়ের ছবি।
আমি নন্দিতা। হাঁটু মুড়ে বসতে-বসতে বলল সে। অভিজিৎ সমদ্দার আমার দাদা।
ওহ, তুমি অভিজিতের বোন? আমি কিছুটা বিস্ময় নিয়ে তাকালাম। কেননা অভিজিতের এমন সুন্দরী একটা বোন রয়েছে, কখনও বলেনি সে। আমি চোখ সরাতে পারলাম না।
ক্লাস নাইনে পড়ে নন্দিতা। ঠিক যেন একটা পরী। খুব অল্পদিনের মধ্যেই ওর সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। আমাদের নিয়মিত দেখা হতে লাগল ওই খেজুর বাগানে। ক্রমেই ও সুন্দরী থেকে আরও সুন্দরী হয়ে উঠল। একদিন। নন্দিতা বলল তার কেমন বমি-বমি লাগছে। আমি ভয়ে পালালাম। সেই শেষ দেখা।
বিয়ে কবে বললি? কাল? কীভাবে যাব? এত অল্প সময়ে! তা ছাড়া ছুটি নেয়া…অনেক ঝামেলার ব্যাপার।
তুই ইচ্ছা করলে পারবি। তুই-ই পারিস। আগেও পেরেছিস।
কিন্তু…
কীসের কিন্তু? কোন কিন্তু না। নন্দিতার বিয়ে বলে কথা। তুই না থাকলে হয়?
এতদিন পর-
নন্দিতা খুব করে বলছিল তোর কথা। মেয়ে মানুষের মন তো, কখন কী আবদার করে বলা মুশকিল। পুরানো প্রেম-ভুলতে পারে না।
এসব বলে লজ্জা দিস না। জাস্ট একটা অ্যাকসিডেন্ট।
অ্যাকসিডেন্ট না কী ছিল সে প্রসঙ্গ থাক। আমি যদি তোকে তখন পেতাম, স্রেফ পুঁতে ফেলতাম। বাদ দে সেসব। তাতুয়াকান্দা, গ্রামের নাম। নাম শুনেছিস তো?
না।
নারায়ণগঞ্জের মধ্যে। আড়াইহাজারে।
ও।
গুলিস্তান থেকে বাসে উঠবি। আড়াইহাজার নেমে খানাকান্দা যাবি।
তুই না বললি তাতুয়া—
তাতুয়াকান্দা।
হুম। ওদিকটায় যাইনি কখনও।
খুব সুন্দর জায়গা। গেলে ভাল লাগবে। অনেকদিন পর নন্দিতাকে দেখবি। আরও ভাল লাগবে। এ কী! তুই তো লজ্জায় মুখ লাল করে ফেলছিস। তুই যদি একবার আমাকে আভাস দিতি নন্দিতাকে তোর ভাল লাগে, আমিই তোর সাথে ওর বিয়ের ব্যবস্থা করে দিতাম। আমার কাছে ধর্মটা কোন ব্যাপার না। কিন্তু বোনটা আমার অনেক কষ্ট পেয়েছিল! একমাত্র বোন। খুব আদরের।
প্লিজ, অভিজিৎ।
হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আড়াইহাজার থেকে টেম্পোতে যাবি খানাকান্দা। খানাকান্দা বাজারে নন্দিতা স্টোরে যাবি। ওখানে দোকানের পরিমল তোকে মোটর সাইকেলে করে আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাবে। ওকে বলে রাখব। তাতুয়াকান্দা ওখান থেকে কাছেই।
আচ্ছা।
মিস করিস না। চলে আয়। খুব ভাল লাগবে।
আসব।
আমি যাই। আরও কয়েক জায়গায় দাওয়াত দিতে হবে।
আচ্ছা।
চলে গেল অভিজিৎ।
আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট খেলাম। রিকশা ঠিক করতে যাব এমন সময় বেজে উঠল মোবাইল। দেখি সাজ্জাদ ভাইয়ের ফোন। প্রথমে ভাবলাম ধরব না। কিন্তু পরে। ধরলাম।
হ্যালো, রাজেশ?
জি।
এলেন না তো?
আমি এক ঘণ্টা আগেই এসেছি। আপনার অফিসটা নেই। ফোনও বন্ধ। চলে যাচ্ছি। বাই।
কেন, কী হলো? সাজ্জাদ ভাই বললেন, আমার অফিসে আসলে নেটওয়ার্কের সমস্যা। আমিও ট্রাই করে যাচ্ছিলাম আপনাকে। আসুন, অনেকদিন গল্প হয় না। আপনি ঠিক কোথায় আছেন, বলুন তো? আমি নিজে আসছি।
আমি আমার অবস্থান জানালাম।
সাজ্জাদ ভাই পাঁচ মিনিটের মধ্যে এসে আমাকে নিয়ে গেলেন।
উনি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, ওখানে। আপনার যাওয়া ঠিক হবে না।
আমি জানতে চাইলাম, কেন?
উনি বললেন, প্রথমত জায়গার নামটাই আমার পছন্দ হচ্ছে না। দ্বিতীয়ত, ওই ছেলের সাথে আপনার এতদিন পর দেখা হলো আর দুম করে আপনাকে তার বোনের বিয়ের দাওয়াত দিল, বলল, আপনার কাছেই যাচ্ছিল। নাহ্, আপনি যাবেন না। মতলব ভাল না।
কীভাবে বুঝলেন?
আমি এসব বুঝি। অভিজ্ঞতা। আহসান ভাইকে জিজ্ঞেস করবেন, তিনিও আমার কথার বাইরে যান না।
.
কিন্তু আমি তার কথার বাইরে গেলাম। রাতে শুয়ে-শুয়ে বারবার চোখে ভাসল নন্দিতার ছবি। কী টলমলে চেহারা। টিকালো নাক, টানা চোখ। গোলাপের মত ঠোঁট। আহ! আমাকে নন্দিতার কাছে যেতেই হবে। কতদিন তাকে দেখিনি!
এখন কেমন দেখতে হয়েছে সে? অভিজিৎ বলল আরও সুন্দর হয়েছে। সুন্দর হবারই কথা। আমার সাথে তার যখন সম্পর্ক ছিল তখন সে ক্লাস নাইনে পড়ে। দশ-বারো বছর আগের কথা সেটা। এখন তো পূর্ণ যৌবনা সে। চাকবুম চাকবুম।
খুব সকালেই রওনা দিলাম আমি। এই সকালেও গুলিস্তানে গিজগিজ করছে লোকজন। ফেরিওয়ালারাও যথারীতি তৎপর।
ভাল একটা সিট নিয়ে বসে পড়লাম। বাস ছাড়ল। জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছি। খুব ভাল লাগছে। ঢাকা থেকে যত দূরে সরে যাই, তত ভাল লাগে সবকিছু। সবসময়ই আমার এমন অনুভূতি হয়।
বাসে আড়াইহাজারে নেমে টেম্পোতে খানাকান্দা গেলাম। এক ভ্যানওয়ালা জিজ্ঞেস করল, স্যর কি লালুর কান্দি যাবেন? নাকি ডোমারচর?
বললাম, তাতুয়াকান্দা।
সে বলল, তা হলে ভ্যানে ওঠেন। আমার বাড়ি কাকাইল মোড়া।
আমি বললাম, আমি আসলে এদিকের কিছুই চিনি না। এই প্রথম এসেছি। তবে সমস্যা নেই। আমাকে নিয়ে যাওয়ার লোক আছে। এখানে নন্দিতা স্টোরটা কোনদিকে বলতে পারো?
পারুম না কেন? ওই যে মাঠের ওই পাশে একটা স্বর্ণবন্ধক দোকান আছে, তার ওপাশে। উনার ভাইটারে তো আমিই এই ভ্যানে করে শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিলাম।
কী জন্য?
কী জন্য মানে? পোড়াইতে। অ্যাক্সিডেন্টে যা-তা অবস্থা হয়েছিল।
আমি সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। নন্দিতার ভাই?
জি। উনার ভাই।
অভিজিৎ?
জি। ওটাই তার নাম ছিল। একটাই তো ভাই।
কী বলছ?
আপনি চিনতেন?
আমি তার উত্তর না দিয়ে বললাম, কবের ঘটনা?
ভ্যানওয়ালা উত্তর দিল, এই ধরেন বছর তিনেক আগে।
অভিজিৎ?
জি। একটাই তার ভাই।
আমি দাঁড়ানো থেকে বসে পড়লাম।
ভ্যানওয়ালা বলল, স্যর কি অসুস্থ?
ঘামছি আমি। সেই সাথে মনের মধ্যে বয়ে যেতে লাগল দুশ্চিন্তার স্রোত। গতকাল আমাকে নন্দিতার বিয়ের দাওয়াত দিতে গিয়েছিল অভিজিৎ। অথচ তিন বছর আগে সে মরে গেছে! আমি পুরো ব্যাপারটা স্বপ্ন দেখিনি তো? তা কীভাবে সম্ভব? সাজ্জাদ ভাইয়ের অফিসে কাল আড্ডা দিয়েছি। এখানে আসার ব্যাপারে উনি নিষেধ করছিলেন। তা ছাড়া অভিজিৎ ঠিকানা না দিলে আমার জানার কথা নয় যে এখানে ওদের বাড়ি।
স্যর কি অসুস্থ? ভ্যানওয়ালা আবার জিজ্ঞেস করল।
না, হঠাৎ মাথা ঘুরে উঠেছিল। এখন ঠিক আছি, আমি উঠে দাঁড়ালাম। তখনও দুর্বল লাগছে।
স্যর, ওই দোকানের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। কিছু। কিনবেন? নাকি এমনি?
এমনি।
ওহ। এখানে নতুন কেউ এলে ওই দোকানের কথা জানতে চায়।
কেন?
অনেক জিনিস পাওয়া যায় তো, তাই। এখানকার সবচেয়ে বড় দোকান।
দোকানটা কে চালায়?
আগে অভিজিই চালাইত। সে মরার পর তার এক ভাগ্নে চালায়।
পরিমল?
স্যর তো চিনেন দেখছি।
একটু পর দেখলাম একটা রোগা-পাতলা ছেলে ধীর গতিতে একটা মোটর সাইকেল চালিয়ে আমাদের দিকে আসছে। আমার কাছে এসে থামল।
স্যর, আপনি রাজেশ স্যর? ছেলেটি বলল।
হ্যাঁ, মাথা কঁকালাম আমি। তুমি পরিমল?
পরিমল বাবু অসুস্থ। আমাকে পাঠালেন আপনাকে নিতে। পেছনে ওঠেন, স্যর। আমি নিয়ে যাচ্ছি।
আমি মোটর সাইকেলের পেছনে উঠে বসলাম। ভ্যানওয়ালা এগিয়ে এসে বলল, স্যরকে কই নেন?
ছেলেটি বলল, কোথায় নিই, তোর কী? কথা কম কস, রমজান। একেবারে চোখ গালাইয়ে দিমু।
.
গ্রামের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি। রাস্তার দুপাশে বাঁশ ঝাড়। মানুষজন খুব একটা চোখে পড়ল না। আস্তে-আস্তে মোটর সাইকেল চালাতে লাগল ছেলেটা। হঠাৎ বলল, এ দিকটায় শেয়ালের উৎপাত খুব বেশি।
আমি বললাম, শেয়াল তো এখন কোথাও তেমন দেখা যায় না।
ছেলেটি বলল, আশপাশের গ্রামগুলোতে গত কয়েকদিন ধরে শেয়ালের উৎপাত এমন বেড়েছে যে বলার নয়। সামনে যাকে পাচ্ছে তাকেই আক্রমণ করছে। লালুর কান্দি, ডোমারচর নয়নাবাদ, উলুকান্দি, পাঁচগাঁও…
আমি এসব নামও শুনিনি।
রাতেই ঘটনা ঘটে। রাতে বাড়ি থেকে না বেরোনোই ভাল।
এদিকে স্বাস্থ্য কেন্দ্র নেই?
আছে। একজন মেডিক্যাল অফিসার কী করবে?
.
বেশ পুরানো দোতলা একটি বাড়ির সামনে এসে ছেলেটি মোটর সাইকেল থামাল।
বাড়ির চারপাশ গাছগাছালিতে ভরা। অনেকদিন পরিষ্কার করা হয় না। গেটের সামনের ছোট্ট পাকা জায়গাটায় শেওলা জমে পিচ্ছিল হয়ে আছে। এটা একটা বিয়ে বাড়ি মনেই হচ্ছে। না। আশপাশেও কোন বাড়িঘর দেখছি না। দু-তিনটা ঘর পড়ে আছে, সেগুলো ছনের এবং ভাঙা।
ছেলেটি যেন আমার মনের কথা টের পেল। বলল, এসব জায়গা বাবুজিদের।
বাবুজি? আমি প্রশ্ন করলাম।
অভিজিৎ বাবুদের। সে আঙুল উঁচিয়ে আশপাশটা দেখাল। এসব জমিজমা সবই বাবুদের।
ওহ।
ভেঙে যাওয়া ঘরগুলোতে গরু-বাছুর থাকত।
আচ্ছা।
ঝড়ে ভেঙে গেছে। পরে আর ঠিক করা হয়নি।
ওহ।
চলুন ভেতরে যাই।
চলল।
ছোট্ট লোহার গেট তালা মারা। কোমর থেকে চাবির গোছা বের করে তালা খুলতে লাগল ছেলেটি।
আমার নাম দয়াল, তালা খুলতে-খুলতে বলল সে। আমার মোবাইল নম্বর রাইখে দিয়েন। যে কোন দরকারে ফোন করবেন।
বাড়িতে কেউ নেই?
থাকবে না কেন? আছে। দিদি গেছে তার পিসী বাড়ি। ওখানেই তাকে সাজাইব। লগ্ন ছাড়া কি বিয়ে হয়? লগ্ন রাত দুইটায়। তখন বিয়ে হইব। সন্ধ্যার পরেই চইলা আইব সবাই। আর বড় বাবু গেছে দই আনতে। একটু পরেই চইলা আইব।
বড় বাবু মানে? নন্দিতার বাবা?
উফ। শালার ইন্দুরে কামড় দিছে। আমার কথার উত্তর না দিয়ে ডান হাতের বুড়ো আঙুল মুখের মধ্যে নিয়ে চুষতে লাগল দয়াল। সাবধানে থাইকেন। ঘরে ইন্দুর আছে। একবার এক বাচ্চারে খাইয়া ফেলাইছিল।
শুনে আমি থমকে গেলাম। আরও থমকে গেলাম কী নির্বিকারভাবে বলে যাচ্ছে ছেলেটি।
পুরা শরীর তখনও খায় নাই। অর্ধেকটা সবে খাইছে। নাড়িভুড়ি বেরোয়ে গেছিল। এই ধরেন গত বছরের ঘটনা। সবাই জানে।
আরেকটু হলেই আমি বমি করে ফেলছিলাম।
ছেলেটি গেট খুলে আমাকে ভেতরে নিল। তারপর দরজার তালা খুলল। পুরানো ভাপসা গন্ধ ঝাঁপটা মারল নাকে। জুতা খুইলা ঘরে ঢোকেন। ছেলেটি নিজের পায়ের স্যাণ্ডেল দেয়ালের এক পাশে রেখে বলল।
আমি জুতো-মোজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম।
চমৎকার সাজানো ঘর। একেবারে ঝকঝকে-তকতকে। বিশাল নকশাওয়ালা পালঙ্ক। পুরু গদি। টানটান করে ওপরে চাদর বিছানো। পাশাপাশি দুটো বালিশ। পুরানো আমলের সোফা। সামনে টি টেবিল। সবকিছুই পরিষ্কার। তবু কেমন। একটা গন্ধ যেন।
আপনি এ ঘরেই শোবেন। বলল ছেলেটি। টর্চ আছে। সাথে? না থাকলে ওই টেবিলের ড্রয়ারে পাবেন। হাত দিয়ে কোনার একটি পড়ার টেবিল দেখাল সে। পল্লী বিদ্যুৎ। দুই ঘণ্টা কারেন্ট থাকে, আবার দুই ঘণ্টা থাকে না। টেবিল ল্যাম্প আছে, জ্বালাইয়ে নিয়েন। আমি সামনের, ওই ভাঙা ঘরে থাকব। কোন দরকারে মোবাইলে কল দিয়েন। এত দূরে, ডাকলেও শুনব না। দোতলায় যাইয়েন না। দোতলায় দিদির ঘর। আপনি আইবেন বলে বড় বাবু এই ঘর ছাড়ছে। উনি থাকবেন চিলেকোঠার ঘরে। এক নাগাড়ে বলে গেল ছেলেটি।
এই যে আপনার ব্যাগ রাখলাম।
আমার ব্যাগ একটা চেয়ারের উপর রাখল সে।
বাথরুম ওইটা দেইখা নেন, ছেলেটি বলল। শ্যাম্পু, সাবান সব আছে। গ্রাম হইলে কী হইব, পানি গরম করার ব্যবস্থা আছে। স্নান সাইরা খাইয়া-দাইয়া ঘুম দেন। ক্লান্ত লাগতাছে আপনারে। তা ছাড়া রাত জাগন লাগব। রাতেই তো বিয়া। আসেন, আপনের খাবার টেবিল দেখাইয়ে দিই।
আমাকে পাশের রুমে নিয়ে গেল সে।
বিশাল ডাইনিং টেবিল। প্রায় অর্ধেকটাই পূর্ণ হয়ে আছে। খাবারে। সব ঢাকনা দেয়া।
টাটকা রান্না করা। ভোরবেলায় রান্না করেছি, ছেলেটি বলল। যা মন চায় নিয়ে খাবেন। একটা বাটিতে শুয়োরের কলিজা আছে। আপনি মুসলমান। ওইটা খাবেন না জানি। তবু রাখছি যদি টেস্ট করেন। তবে ইলিশ মাছটা খাইয়েন। কোন ভেজাল নাই। ঘি দিয়া ভাজছি। পুরা আস্তা ইলিশ। হেভি টেস্ট পাবেন। মুরগির মাংসের তিনটা পদ আছে। পরে বইলেন কোনটা ভাল লাগছে। ছাগলের মাংসটা ফাটাফাটি রানছি। খাইয়েন।
আমি কখনওই খাবার রসিক নই, তাই কিছু বললাম না। শুধু শুনে গেলাম।
ছেলেটি যাওয়ার আগে তার মোবাইল নম্বর আমাকে দিয়ে গেল। বলে গেল, যে কোন দরকারে আমারে ফোন কইরেন। আমার নাম দয়াল।
আমি দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে কাপড়-চোপড় ছাড়লাম। দুপুর দুটো বেজে গেছে। ভাবলাম গোসল করে ফ্রেশ হয়ে তারপর লাঞ্চ করব। বাথরুমে ঢুকলাম। শাওয়ার ছেড়ে মনের সুখে গোসল করলাম। ঠাণ্ডা পানির পরশে দেহমন। জুড়িয়ে গেল। তরতাজা হয়ে উঠল শরীর।
গুনগুন করে গান গাইতে-গাইতে বাথরুম থেকে বেরোলাম। এবং বিছানার দিকে চোখ পড়তেই জমে গেলাম। আমার হাত থেকে ভেজা কাপড়গুলো মেঝেতে পড়ে গেল। বিছানায় দুপা তুলে বসে আছে অভিজিৎ!
মনে হলো আমার গলার কাছে হৃৎপিণ্ডটা উঠে এসেছে। ধকধক করছে। নিজেই শুনতে পাচ্ছি নিজের হৃৎপিণ্ডের ধুকধুকানি শব্দ।
কী রে? এভাবে তাকিয়ে আছিস কেন? মনে হয় ভূত দেখছিস! হাসল অভিজিৎ। বিছানা থেকে নামল। এই প্রথম খেয়াল করলাম সে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে হাঁটে।
তুই-তুই কোত্থেকে এলি? আমি নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম।
কোত্থেকে এলাম মানে? আমি দোতলায় ঘুমোচ্ছিলাম। তুই এসে ডাকলিও না। পথে কোন সমস্যা হয়নি তো? এখানে, আসতে কোন অসুবিধা
না, না, কোন সমস্যাই হয়নি। বরং সবাই খুব হেলপফুল।।
তুই খেয়ে রেস্ট নে। একটা ঘুম দে। ভাল লাগবে।
আয়, তুইও খা আমার সাথে। একসাথে খেতে-খেতে গল্প করি।
না রে। উপোস রয়েছি। একমাত্র বোনের বিয়ে। বড় ভাই হিসাবে কত দায়িত্ব থাকে। হাসল অভিজিৎ। কেন জানি আমার সেই হাসি ভাল লাগল না।
কাপড়গুলো বারান্দায় গিয়ে একটা দড়িতে মেলোম। আকাশে মেঘ জমছে। এত বড় বাড়িতে মাত্র দুজন প্রাণী থাকে। অভিজিৎ ও নন্দিতা। অভিজিতের বাবা কি এই বাড়িতে থাকেন না, নাকি আগেই মারা গেছেন। মাথার মধ্যে নানা প্রশ্ন খেলছে। গতকাল অভিজিতের দাওয়াত দেয়া থেকে শুরু করে এখানে আসা-ভ্যানওয়ালার কথাগুলো-ভ্যানওয়ালা কি মিথ্যে বলেছে আমাকে? মজা করেছে? করতেও পারে। গ্রামের এসব অশিক্ষিত মানুষ উল্টোপাল্টা কথা বলে খুব মজা পায়।
ভ্যানওয়ালার কথা মনে পড়তেই নিজের প্রতি রাগ হলো খুব। আমি কি তবে তার কথা বিশ্বাস করে ফেলেছি? কী হাস্যকর! জলজ্যান্ত একজন মানুষকে কেউ মৃত বলল, আর আমার মত উচ্চশিক্ষিত একজন মানুষ সেটাকে বিশ্বাস করে কত কী ভাবতে শুরু করেছি।.ভ্যানওয়ালা বলেছিল তার ভ্যানে করে অভিজিতের লাশ পোড়াতে নিয়ে যাচ্ছিল শ্মশানে। সে বলল, আর আমিও বিশ্বাস করলাম। কী সব ফালতু কথা। হাস্যকর।
কাপড় মেলে এসে দেখি অভিজিৎ সেভাবেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। এক পায়ে ভর দিয়ে।
নন্দিতা একেবারে সেজেগুজেই আসবে, পায়ের ভর বদল করে বলল সে। ওর জন্য অপেক্ষা করে লাভ নেই। তুই খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে নিস। সন্ধ্যায় উঠলেই হবে।
বর কী করে? প্রশ্ন করলাম আমি।
দাঁত বের করে হাসল অভিজিৎ। তার হাসিটা যে এত বিশ্রী লাগে দেখতে-আমার জানা ছিল না।
বায়ো মেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার, বলল অভিজিৎ। ছেলেটা ভালই। আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। নন্দিতাই পছন্দ করেছে। কপালে ডাক্তার জুটল না তো, তাতে কী? ওই লাইনেরই ইঞ্জিনিয়ার ধরেছে।
আমি কিছু বললাম না।
অভিজিৎ বলল, তোর বউ কী করে?
আমি বললাম, আমি তো বিয়েই করিনি। বউ আসবে কোত্থেকে?
অভিজিৎ বলল, তা হলে তো আরও ভাল হলো। ওই ছেলে না এলে তোর হাতেই নন্দিতাকে তুলে দেয়া যাবে। অবশ্য তুই যে মানের লুচ্চা, নন্দিতা রাজি হবে বলে মনে হয় না।
আমি বললাম, দেখ, অভিজিৎ, এভাবে বারবার আমাকে
হা-হা করে হাসল অভিজিৎ, কেন জানি না শিউরে উঠলাম আমি।
একাই খেলাম আমি। চমৎকার সব রান্না। অভিজিৎ খেল না। দোতলায় চলে গেল।
খেয়ে-দেয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। প্রায় সাড়ে তিনটা বাজে। মোবাইল বের করলাম। এখন পর্যন্ত একটাও কল আসেনি। দেখলাম স্ক্রিনে ইমার্জেন্সি লেখা। অর্থাৎ নেটওয়ার্ক নেই। বুঝলাম এদিকটায় মোবাইলের টাওয়ার নেই। কয়েকবার অফ-অন করলাম মোবাইল। লাভ হলো না। বালিশের নিচে মোবাইল রেখে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।
হঠাৎ করেই আমার ঘুম ভেঙে গেল।
ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম।
প্রচণ্ড পিপাসায় বুক ফেটে যাচ্ছে।
ঘড়ির দিকে তাকালাম। রাত নটা বেজে গেছে!
এতক্ষণ আমি ঘুমিয়েছি!
কেউ ডাকল না আমাকে?
কোলাহলের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। মনে হলো ঘরের বাইরে। একসঙ্গে অনেক মানুষ কথা বলছে। ঘরের বাইরে নাকি দোতলায়? মনে হচ্ছে তর্ক-বিতর্ক চলছে কিছু নিয়ে। আসলেই? নাকি কল্পনা? আমি বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম। মুহূর্তে সব শব্দ থেমে গেল। ঘরে অল্প পাওয়ারের বাতি জ্বলছে।
আমি টেবিলের কাছে গিয়ে জগ থেকে পানি ঢেলে খেলাম। কেমন যেন অস্বস্তি লাগছে।
জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালাম। নিকষ অন্ধকার।
এটা একটা বিয়ে বাড়ি, সেটা মনেই হচ্ছে না।
কোন আয়োজন নেই, কোন অতিথি নেই, এমনকী এখন পর্যন্ত নন্দিতারও কোন দেখা নেই।
অভিজিৎ বলেছে, লগ্ন রাত দুটোয়। আসলেই কি তাই?
আমি অবশ্য এসব লগ্নের বিষয় জানি না। বুঝিও না। নিজের ধর্মেরই খোঁজ রাখি না-আবার অন্যের ধর্ম!
আবার কোলাহলের শব্দ শুনলাম। কান খাড়া করলাম। আমি। মনে হলো কারা যেন ধাক্কাধাক্কি করছে। প্লেট ভাঙার শব্দ হলো। চেয়ার আছড়ে পড়ল কোথাও। কেউ একজন আউ করে উঠল। আমি ঘরের ভেতর চোখ বুলালাম। সব কেমন স্থির। খুব বেশি স্থির। আমি পা টিপেটিপে দোতলার সিঁড়ির কাছে গেলাম। দোতলায় নন্দিতার ঘর।
একটু ইতস্তত করলাম আমি। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলাম। কতদিন নন্দিতাকে দেখিনি।
দোতলায় উঠে বড় ধরনের ধাক্কা খেলাম। নিচ থেকে আসা আবছা আলোয় দেখলাম দরজায় বড়সড় একটা তালা মারা। দুপুরে অভিজিৎ বলছিল সে এ ঘরেই ছিল, তা হলে কি তালা মেরে বাইরে গিয়েছে? আমার ঘরে ডিম লাইটটাও কি জেলে রেখে গেছে সে? আমি তালার গায়ে হাত রাখলাম। মনে হলো ধুলো পড়ে আছে।
মনের অজান্তে আমি জোরে চিৎকার দিলাম, অভিজিৎ!
সারা বাড়িতে প্রতিধ্বনি তুলল আমার ডাক।
আমি আবার চিৎকার দিলাম, অভিজিৎ!!
দেয়ালে-দেয়ালে বাড়ি খেল সেই শব্দ।
আমি দ্রুত নিচে নেমে এলাম। ভয় পেয়েছি আমি!
তাড়াতাড়ি প্যান্ট-শার্ট পরে নিলাম।
দ্রুত জুতো জোড়া পরে দরজার ছিটকিনির দিকে হাত বাড়ালাম। ছিটকিনি খোলা। খোলাই তো থাকবে। দয়াল আমাকে এখানে রেখে চলে যাবার পর আমি তো ছিটকিনি আটকাইনি।
আমি দরজা টান দিয়ে খুললাম। বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস ঝাঁপটা মারল আমার মুখে। ছোট্ট লোহার গেট। ওটা টান দিলাম। বন্ধ। দয়াল কি বাইরে থেকে আমাকে আটকে দিয়ে গেছে? আমি পাগলের মত লোহার গেটটি টানতে লাগলাম। পাল্লা নড়াতে পারলাম না এক চুলও। দৌড়ে ঘরে ঢুকলাম। বালিশের নিচ থেকে মোবাইল বের করলাম। দয়ালকে রিং করলাম। রিং যাচ্ছে না। নেটওয়ার্ক নেই। আবার দৌড়ে এসে দরজার বাইরের গেট টানাটানি করলাম। আবার ঘরে ঢুকলাম। এবার জানালার গ্রিল ধরে টানতে লাগলাম যদি খুলে আসে! হাত ব্যথা করে ফেললাম, তবু নড়াতে পারলাম না, এমন মজবুত।
জানালায় মুখ নিয়ে চিৎকার করলাম, বাইরে কি কেউ আছেন?
কোন উত্তর এল না।
শুধু বাতাসের শোঁ-শোঁ শব্দ।
ক্রমেই বাড়তে লাগল বাতাস। জানালার পর্দা উড়ে যেতে চাইল। ঝড় শুরু হয়েছে!
আমি জানালা বন্ধ করে দিলাম।
কড়াৎ করে কাছেই কোথাও বাজ পড়ল। আমি কেঁপে উঠলাম। উঠে দ্রুত ঘরের সব লাইট জ্বেলে দিলাম। উজ্জ্বল আলোয় ঘরটা ভরে উঠল। এতে ভয় কিছুটা কমলেও বুকের ধুকপুকানি টের পাচ্ছি। ঘরের চারপাশে চোখ বুলাতে লাগলাম অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ে কিনা। না, তেমন কিছুই নেই। নিজেকে বুঝ দেয়ার চেষ্টা করলাম আসলে যা দেখেছি সব স্বপ্ন। অথবা সবই স্বাভাবিক। অযথা আমি ভয় পাচ্ছি।
বাইরে প্রচণ্ড বাতাস। গাছের ডাল বাড়ি খাচ্ছে জানালায়। এমন ঝড় হতে থাকলে যে কোন সময় কারেন্ট চলে যেতে পারে। আমি টেবিলের কাছে গিয়ে মোমবাতি আছে কিনা খুঁজতে লাগলাম। ম্যাচ আমার পকেটেই আছে।
টেবিলে কোন মোমবাতি নেই।
টান দিয়ে ড্রয়ার খুললাম। পুরানো কলম। একটা ভাঙা পেন্সিল। নিচের ড্রয়ার খুললাম। চার-পাঁচটা পুরানো ছেঁড়া বই। আতিপাতি করে খুঁজলাম। কোথাও কোন মোমবাতি নেই। অথবা বিকল্প কিছু।
ধীরে-ধীরে ঝড়ের গতি বাড়ছে।
আলোও কেঁপে-কেঁপে উঠল কয়েকবার। হঠাৎ দপ করে নিভে গেল।
গাঢ় অন্ধকারে ভরে গেল রুম।
শুধু ঝড়ের শব্দ।
হঠাৎ আমার পায়ের ওপর দিয়ে কী যেন চলে গেল। আমি ভয়ে চিৎকার দিলাম। বুঝলাম ওটা ইঁদুর। দ্রুত পকেট হাতড়ালাম। ম্যাচ খুঁজে পেলাম না। শার্টের পকেট, প্যান্টের পকেট বারবার হাতড়াতে লাগলাম। কোথাও ম্যাচ নেই। আসার সময় সম্ভবত কোথাও পড়ে গেছে।
মোবাইলটা হাতে নিলাম। বাটনে চাপ দিতে অল্প আলো জ্বলল। মোবাইলের টর্চ জ্বালানো ঠিক হবে না, দ্রুত চার্জ চলে এমন অবস্থা হবে, আগেই চার্জ দিয়ে রাখতাম।
মোবাইলের আলোয়, খাটে বসে রইলাম। অভিশাপ দিলাম ভাগ্যকে। সাজ্জাদ ভাইয়ের কথা শোনা উচিত ছিল। মনে হচ্ছে রাতে আর কারেন্ট আসবে না। মোবাইলের চার্জটুকু শেষ হয়ে গেলে কী হবে?
নাহ্, মিছেমিছি ভাবছি। নিজেকে সান্ত্বনা দিলাম। কিছুই হয়নি, বেশি-বেশি চিন্তা করছি আমি। হয়তো নন্দিতা সত্যিই তার পিসীর বাড়িতে-হয়তো ওখানেই বিয়ের আয়োজন হচ্ছে, হয়তো ধর্মীয়ভাবে ঝামেলা হতে পারে মনে করে অভিজিৎ আমাকে না ডেকেই সেখানে চলে গেছে। আর অভিজিতের সাথে আমার সত্যিই দেখা হয়েছে, এখানে উল্টোপাল্টা কিছু ভাবার সুযোগ নেই। আর যদি উল্টোপাল্টা কিছু হত, দয়াল নিশ্চয়ই আমাকে এখানে আনত না। আর ওই ভ্যানওয়ালা যা বলেছে, নিশ্চয়ই তার মাথার ঠিক নেই। গ্রামের দিকে এ ধরনের অনেক লোক আছে, খুব উল্টোপাল্টা বলে। নতুন লোক দেখলে এ ধরনের কথা বলে মজা পায়।
মোবাইলের আলো আস্তে-আস্তে ক্ষীণ হয়ে আসছে। বুঝতে পারছি বেশি চার্জ নেই। বাইরে কি ঝড় থেমে গেছে? আর কোন শব্দ পাচ্ছি না। শুধু টিপটিপ একটু বৃষ্টির আওয়াজ। গেটে মনে হলো ঠকঠক শব্দ হলো। কান খাড়া করলাম। না, আর কোন শব্দ নেই। শেয়াল বা কুকুর হতে পারে। আবার কোথাও কোলাহলের শব্দ পেলাম, চিৎকার, চেঁচামেচি। আবার নিশ্চুপ।
বিছানা থেকে উঠলাম। মোবাইলটা মনে হয় আর কিছুক্ষণ পরেই বন্ধ হয়ে যাবে।
টেবিলে গিয়ে বসলাম।
এক কোনায় পুরানো খবরের কাগজ। কিছুটা দোমড়ানো।
অনিচ্ছা সত্ত্বেও খুললাম। যদি কিছুটা সময় কাটানো যায়।
দেখি প্রথম পৃষ্ঠায় পুড়ে যাওয়া এক গাড়ির ছবি। নিচে বড় হেডলাইন-মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় বালু ব্যবসায়ীর মৃত্যু।
পড়তে লাগলাম খবরটা।
গতকাল আনুমানিক রাত একটার দিকে নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার খানাকান্দা ইউনিয়নের তাতুয়াকান্দা গ্রামের বিশিষ্ট বালু ব্যবসায়ী শ্রী অরিন্দম দাসের পুত্র শ্রী অভিজিৎ দাস এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হন। উল্লেখ্য তিনি তার বোনকে নিয়ে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন। গাড়িটি তিনি নিজেই ড্রাইভ করছিলেন। গাড়ি যোগার দিয়া নামে এক গ্রামের পথ দিয়ে যাওয়ার সময় পেছন থেকে বালুবাহী একটি ট্রাক ধাক্কা মারে, গাড়িটি উল্টে গভীর খাদে পড়ে যায় ও গাড়িটিতে আগুন ধরে যায়। অভিজিতের লাশ উদ্ধার করা সম্ভব হলেও তার বোনের লাশ পুড়ে গাড়ির সিটের সাথে লেগে থাকে। তার বোনের নাম নন্দিতা রানি দাস। পুলিশ বলছে
আর পড়তে পারলাম না। মোবাইলের আলো নিভে গেল।
কত রাত এখন? একটা নাকি দুটো?
কোথাও কোন শব্দ নেই।
শুধু বাইরে দুএক ফোঁটা বৃষ্টির শব্দ।
অসহায়ের মত অপেক্ষা করতে লাগলাম।
আমি জানি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই অভিজিৎ আসবে…
এবার একা নয়!
আমার কাছ থেকে যে কষ্ট পেয়েছিল নন্দিতা, তার শোধ কি তুলবে না?
সেই আংটি – মুহাম্মদ শাহেদুজ্জামান
সামনে উবু হয়ে বসে থাকা লোকটার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিল পাভেল। লোকটার কালিঝুলি মাখা মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল। চুল উষ্কখুষ্ক, কতদিন পানি লাগেনি কে জানে! গায়ে একটা ত্যানার মত পাঞ্জাবী, আর লুঙ্গি। বসে বসে গাছের ডাল দিয়ে মাটিতে আকিবুকি কাটছে। এই লোক আবার জ্যোতিশ্চন্দ্র হয় কীভাবে!
ছোটবেলার বন্ধু রুদ্রর কাছে এই জ্যোতিষের সন্ধান পেয়েছে পাভেল এই লোক নাকি বিরাট এলেমদা আদমি। কারও উপর প্রসন্ন হলে তাকে রাজা বানিয়ে দিতে পারেন, আর খেপে গেলে পথের ফকির বানাতেও দেরি হয় না।
দুই বন্ধুর আবার এইসব অতিপ্রাকৃত বিষয়ে ভীষণ আগ্রহ। ছোটবেলায় স্কুল ফাঁকি দিয়ে দুজন ঘুরে বেড়াত বিভিন্ন সাধু-সন্ন্যাসীর আস্তানায়, আর পীর ফকিরের মাজারে। অবশ্য পরীক্ষার প্রশ্ন ফাস করার মতলবে ফকিরদের দ্বারস্থ হওয়ার সেই ভূত পাভেলের মাথা থেকে অনেক আগেই নেমে গেছে। কিন্তু রুদ্র সেই আগের মতই অন্ধভাবে এসবে বিশ্বাস। করে। পরের দিকে পাভেল রুদ্রকে অনেকটা এড়িয়েই চলত। রুদ্রর বাবা বিশাল ধনী, তার ছেলের পক্ষে এসব পাগলামি মানায়। ছাপোষা পরিবারের সন্তান পাভেল। তিনবেলা। ভাতের চিন্তা, সেই সঙ্গে পরিবারের ভার মাথায় চেপে বসলে সেখানে আর কোন খেয়াল রাখার জায়গা থাকে না।
এতদিন পর পাভেল আবার বাধ্য হয়েছে কোন জ্যোতিষীর কাছে আসতে। গত ছয় মাসে তার জীবনে বেশ কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে পরপর। প্রথমে তার বাবা মারা গেলেন, বাবার শোকে তিন মাস পর মা।কয়েকদিন পরেই অফিস থেকে এল বরখাস্তের নোটিশ, কোন কারণ দেখানো হয়নি তাতে। প্রেমিকা তুলির বিয়ে হয়ে গেল মাস খানেক আগে, লণ্ডন প্রবাসী পাত্রের সঙ্গে। পাভেল শুনেছিল বিয়েতে তুলির খুব একটা অমত ছিল না।
এসব ঘটনার যে কোন একটাই বড়সড় ধাক্কা দেয়ার জন্য যথেষ্ট, সেখানে এতগুলো পরপর। হতাশ হয়ে পাভেল এমনকী আত্মহত্যার চিন্তাও করেছিল। ঠিক এই সময়, অর্থাৎ এক সপ্তাহ আগে রুদ্রর আগমন। পাঁচ বছর কোন খবর নেই। তারপরে হুট করে দুপুরবেলা সে পাভেলের বাসায় এসে হাজির। অনেকদিন নাকি পাভেলের সঙ্গে দেখা হয়নি, বন্ধুর জন্য মনটা আনচান করছিল। এসেই পাভেলের মুখ দেখে বুঝে নিল অবস্থা বেশি ভাল না। সবকিছু শুনল রুদ্র পাভেলের মুখ থেকে। তারপর সে এই জ্যোতিষীর ঠিকানা দিয়েছিল পাভেলকে। বলেছিল, এই লোক অনেক বড় গুণী মানুষ। যোগসাধনা করেন, মানুষের চোখে চোখ রেখে তার ত্রিকাল বলে দিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ লোকে সাধনায় অসুবিধা করে বলে লোকচক্ষুর আড়ালে, শ্মশানে-গোরস্থানে পড়ে থাকেন। এই লোককে যদি পাভেল খুঁজে বের করতে পারে তা হলে তিনিই তার সব সমস্যার সমাধান করে দিতে পারবেন। তোর তো এখন আর এসবে বিশ্বাস নেই। কিন্তু এই লোকের দেখা পেলে তোর বিশ্বাস ফিরে আসতে দেরি হবে না। বলেছিল রুদ্র।
হঠাৎ মুখ তুলে পাভেলের দিকে তাকাল লোকটা। কোটরে বসা দুই চোখ, দুটুকরো কয়লার মত জ্বলছে। শয়তানি হাসি সে চোখে। তারপর, লোকটা কথা বলে উঠল।
কী জন্য এসেছিস? তোর কপালটা কি স্কুলের ব্ল্যাকবোর্ড নাকি যে ডাস্টার দিয়ে লেখা মুছে আবার নতুন করে লিখে দেব? কপালের লিখন খণ্ডানো যায় না রে, পাগলা!
অবাক হলো না পাভেল। কে জানে, এই লোকের কাছে যারা আসে তারা হয়তো ভাগ্য বদলানোর ইচ্ছা নিয়েই আসে। বলল, আমাকে রুদ্র পাঠিয়েছে।
ওই পাগলটা? নিজে জ্বালিয়ে শখ মেটেনি, এখন আবার তোকে পাঠিয়েছে আমাকে জ্বালাতে? বলল বটে লোকটা, তবে পাভেল দেখল রুদ্রর নাম শুনে লোকটার মুখ এখন, কিছুটা প্রসন্ন। ব্যঙ্গের একটা হাসি মুখে লটকে বলল লোকটা, তা বলুন, রুদ্রর মহামান্য অতিথি, কী করতে পারি আমি আপনার জন্য?
রুদ্র যা বলল তা যদি সত্যি হয়, তা হলে তো আপনি ত্রিকালজ্ঞ। কিছুই আপনার অজানা নয়। আমি কেন এসেছি আর কীভাবে আমাকে সাহায্য করবেন সেটা আপনিই বলুন। না? কিছুটা তেড়িয়া মেজাজ দেখাল পাভেল।
স্থির দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকল লোকটা পাভেলের দিকে। তারপর আচমকা বাম হাতের তর্জনী আর বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে ওর কপালের দুপাশ চেপে ধরল। পাভেল চমকে লাফিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু লোকটা ওর কপাল চেপে ধরার সঙ্গে সঙ্গে ওর মনে হলো ওর পুরো শরীরটা নরম কাদা দিয়ে তৈরি। নড়াচড়া করার শক্তি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে যেন সে।
যেমন আচমকা পাভেলের কপাল টিপে ধরেছিল তেমন আচমকাই আবার কয়েক সেকেণ্ড পরে ছেড়ে দিল লোকটা। তারপর গড়গড় করে মুখস্থ বলার মত বলে গেল, ছিয়াশিতে জন্ম। ম্যাট্রিক দিয়েছিস দুহাজার দুই-এ। এইচ এস সি দুই বারে পাশ। ভাল চাকরি করতিস। চাকরিটা চলে গেছে। বিয়েটাও ফসকে গেছে। বাবা-মার একজন অথবা দুজনেই মারা গেছে কিছুদিন আগে। আরও বলব? পাভেলের হাঁ করে তাকিয়ে-থাকা মুখের দিকে একটা হাসি ছুঁড়ে দিয়ে বলে গেল লোকটা, যে মেয়েটার সাথে তোর বিয়ের কথা ছিল তার বাম গালে একটা তিল আছে। মেয়েটা নদী ভালবাসে। তোরা ঠিক করেছিলি বিয়ের পর নৌকা নিয়ে দেশের সব কয়টা নদী ঘুরে দেখবি…
লোকটার হাত চেপে ধরল পাভেল। থামুন! ধমকে উঠল ও। যেসব কথা কারও জানার কথা নয় সেসব এই লোক কীভাবে জানে? কে বলেছে আপনাকে এসব কথা? জিজ্ঞেস করল ও।
তুই বলেছিস। এইমাত্র। ফিক ফিক করে হাসছে লোকটা, পাভেলের ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখ দেখে খুব মজা পেয়েছে যেন।
ভাষা হারিয়ে চুপ করে থাকল পাভেল। কিছুক্ষণ পর বলল, তা হলে আপনি এখন বলুন, আমি কী করব?
শোন। উপরে একজন বসে আছে। আঙুল দিয়ে উপরে দেখাল লোকটা। আমরা হচ্ছি তার হাতের সুতোয় বাঁধা পুতুল। সে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে নাচায়। আমরা নাচি। তার ইচ্ছে রদ করার ক্ষমতা কোন বাপের ব্যাটার নেই। লোকটার গলা এখন কিছুটা নরম। আমারও ক্ষমতা নেই তোর জন্যে কিছু করার। সামনে আরও বিপদ আসতে পারে তোর। আমি সেগুলো আটকাতে পারব না। তবে এটা রাখ। এই বলে নোংরা পাঞ্জাবীর পকেটে হাত ঢুকিয়ে কী একটা বের করে পাভেলের হাতটা টেনে নিয়ে খোলা তালুর উপর রাখল লোকটা। জিনিসটা কালো রঙের একটা আংটি। খুব সম্ভব লোহার তৈরি। পাথরের জায়গায় একটা মানুষের মুখ খোদাই করা।
কী হবে এটা দিয়ে? জিজ্ঞেস করল পাভেল।
বাড়ি গিয়ে গোসল করে পরবি আংটিটা। সবসময় এটা পরে থাকিস। বিপদ-আপদ যা আসে আসবে। এই আংটিটা তোর বিপদ কাটাতে না পারলেও তোর মাথা ঠাণ্ডা রাখবে, কীভাবে বিপদ কাটবে সেটা বুঝতে সাহায্য করবে। কখনও খুলবি না। আর এইবার চোখ বন্ধ কর। আমি তিন পর্যন্ত। গোনার পর চোখ খুলবি।
চোখ বুজল পাভেল। লোকটা গুনতে শুরু করল, এক…দুই…তিন।
চোখ খুলতেই পাভেল দেখল, একা একা বসে আছে। সে। সামনে কেউ নেই। আশপাশে যতদূর চোখ যায় কোন জনমানুষের চিহ্ন নেই। স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেন। লোকটা।
.
বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গেল পাভেলের। মধ্যরাতের সুনসান গলি দিয়ে সে যখন বাড়ি ফিরছে তখন হঠাৎ ঘাড়ের কাছটা। শিরশির করে উঠল। পিছনে কার পায়ের শব্দ? ঘুরে তাকিয়ে অবশ্য কাউকেই দেখতে পেল না পাভেল। মনের ভুল ভেবে আবার পা চালাল সে। বাসায় ঢুকেই অবাক হয়ে গেল। পাভেল। বসার ঘরের আলো জ্বলছে। আর সোফায় বসে পা নাচাচ্ছে রুদ্র। পাভেল ঢুকতেই জ নাচাল। কী রে? দেখা হলো জ্যোতিশ্চন্দ্রের সাথে?
তা হয়েছে। কিন্তু তুই ভিতরে ঢুকলি কীভাবে? জিজ্ঞেস করল পাভেল।
অনেকদিন মানবসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন আমি, দোস্ত। নিয়মকানুন সব ভুলে গেছি। পাঁচিল টপকে ঢুকে পড়েছি আর কী। পরে ছাদে উঠে তোদের বাসার ভেতর। ক্ষমাপ্রার্থনার হাসি দিল রুদ্র। এখন বল, কী বললেন জ্যোতিশ্চন্দ্র?
কী বলবেন? এই আংটিটা দিয়ে বললেন সবসময় পরে থাকতে। পকেট থেকে আংটিটা বের করল পাভেল।
আংটিটার দিকে চোখ পড়া মাত্র লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রুদ্র। মুখের ভাব আমূল বদলে গেছে। চোখে যে দৃষ্টি সেটা একমাত্র ছাগলের দিকে তাকিয়ে থাকা ক্ষুধার্ত বাঘের সঙ্গেই তুলনা করা চলে। দেখি আংটিটা! পাভেলের দিকে হাত বাড়িয়ে চাপা গলায় হুঙ্কার ছাড়ল সে।
ত-তুই এরকম করছিস কেন? রুদ্রর ভাবভঙ্গি দেখে ভড়কে গেছে পাভেল।
আংটিটা দে আমাকে! আবার গর্জে উঠল রুদ্র। মনে হলো বুকের অনেক গভীর থেকে উঠে এল গর্জনটা। গলার স্বরও বদলে গেছে তার। কেমন, ঘড়ঘড়ে, জান্তব আওয়াজ। চোখ দুটো জ্বলছে জ্বলজ্বল করে।
কী মনে হলো পাভেলের, আংটিটা মুঠোয় ভরে ফেলল সে। তারপর, হঠাৎ করে রুদ্রর বাড়ানো হাতের দিকে চোখ গেল তার। বহুদিনের পচন ধরে শুকিয়ে যাওয়া মড়ার মত শুকনো, কোঁচকানো সে হাতের চামড়া আঙুলের মাংসহীন হাড়গুলো জড়িয়ে রেখেছে। বড় বড় লোম উঠেছে এখানে সেখানে। পাঁচটা আঙুলের মাথায় তীক্ষ্ণ, বাকানো নখ! এ গলা শুকিয়ে এল পাভেলের। এ আর যে-ই হোক, রুদ্র নয়! প্রচণ্ড অবিশ্বাসে পিছু হটতে গিয়ে সোফায় হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল সে। ওদিকে রুদ্রর মুখেও পরিবর্তন আসতে শুরু করেছে। স্বাভাবিক চেহারা দ্রুত বদলে রূপ নিচ্ছে এক ভয়াবহ দানবে। মুখের চামড়ায় কালচে রং ধরল, তারপর পচে গলে গিয়ে খসে পড়তে শুরু করল চামড়া। একটা চোখ কোটর থেকে খসে বাইরে ঝুলে পড়ল, চোয়ালের চামড়া দুফাঁক হয়ে বেরিয়ে এল তীক্ষ্ণ শ্বদন্ত। লকলকে জিভ বেরিয়ে ঝুলে পড়ল মুখের এক পাশ দিয়ে। দমকা বাতাসের একটা ঝাঁপটার সঙ্গে পাভেলের উপর ঝুঁকে এল শয়তানটা। দে আংটিটা!
আংটি দেবে কী, পাভেল তখন ভয়ে আধমরা। থরথর করে কাঁপছে তার পুরো শরীর। দানবটা ধীরে-ধীরে পাভেলের মুখের কাছে মুখ নিয়ে এল। এত কাছে যে বিচ্ছিরি পচা গন্ধ এসে ধাক্কা মারল পাভেলের নাকে। যে কোন মুহূর্তে জ্ঞান হারাবে সে। তারপর, হঠাৎ করে পাভেলের উপর থেকে সরে গেল বীভৎস মুখটা। মনে হলো কে যেন এক টান মেরে সরিয়ে নিয়ে গেল। তৃতীয় এক ব্যক্তি এসে ঢুকেছে ঘরে। সেই জ্যোতিষী!
রুদ্রবেশী দানবটার ঘাড় ধরে তাকে টেনে সরিয়ে এনেছে। লোকটা। নিষ্ফল আক্রোশে হাত পা ছুঁড়ছে দানবটা, কিন্তু জ্যোতিষীর কোন বিকার নেই। যেন একটা ছমাসের শিশুকে ধরে রেখেছে। তা হলে এই ব্যাপার? এই শয়তান তোর পিছনে লেগেছে? আগেই বোঝা উচিত ছিল আমার! কথা কটা বলে পকেট থেকে একটা শিশি বের করে পাভেলের দিকে ছুঁড়ে দিল লোকটা। এটা খুলে ওর গায়ে ছিটিয়ে দে দেখি!
শিশিটা পাভেলের গায়ে এসে পড়ল। তখনও সংবিৎ ফিরে পায়নি সে। কোনমতে কাঁপা কাঁপা হাতে শিশির মুখ খুলল। ওদিকে, পাভেলের হাতে শিশিটা দেখেই তীব্র আক্রোশে গর্জন করে উঠল দানবটা, আর তার ছটফটানির মাত্রাও বেড়ে গেল দ্বিগুণ।
পাভেল আর দেরি করল না। শিশির ভেতরের তরলটুকু ছুঁড়ে দিল দানবটার গায়ে। মনে হলো আগুন ধরে গেছে, এভাবে চেঁচিয়ে উঠল শয়তানটা। কিন্তু ঘাড়ে চেপে বসে আছে জ্যোতিষীর বজ্রমুষ্টি, একচুলও শিথিল হলো না। ছটফট করতে করতে তীব্র আক্ষেপে ধারাল নখ দিয়ে নিজের গায়ের মাংস খুলে আনতে শুরু করল দানবটা, সেই সঙ্গে চলছে।
পাভেল এতক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে ছিল অবিশ্বাস্য এই দৃশ্যের দিকে। হঠাৎ দেখল, দানবটার জায়গায় ছটফট করছে রুদ্র, সেই পুরানো রক্তমাংসের রুদ্র। মুখ তুলে পাভেলের দিকে তাকাল সে। দোস্ত, বড় কষ্ট হচ্ছে আমার! আমাকে বাঁচা, দোস্ত, আমাকে বাঁচা!
কেমন যেন ঘোর পেয়ে বসল পাভেলকে। ধীরে ধীরে দুপা এগিয়ে গেল সে, উদ্দেশ্য রুদ্রকে জ্যোতিষীর হাত থেকে ছাড়িয়ে নেবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তীব্র ধমক শুনতে পেল, খবরদার! ওর মায়ায় ভুলিস না! বিড়বিড় করে কী যেন বলে তীব্র ঘৃণায় এক দলা থুথু ছিটিয়ে দিল জ্যোতিষী রুদ্রর মুখে। পরক্ষণে আরেকবার বুক ফাটা আর্তনাদ করে উঠল রুদ্র। তারপর দপ করে আগুন জ্বলে উঠল তার শরীরে, নিমিষে পুড়ে ছাই হয়ে গেল সে। ঘরের বাতাসে কেবল ভেসে রইল মাংস পোড়ার তীব্র কটু গন্ধ।
এতক্ষণে হুঁশ ফিরে পেয়ে লোকটার দিকে তাকাল। পাভেল। আ-আ-আ-আপনি… তোতলাচ্ছে সে।
হ্যাঁ, আমি। মুচকি হাসল জ্যোতিষী। দেখা যাচ্ছে ঠিক সময়েই পৌঁছেছিলাম।
কিন্তু আপনি কীভাবে জানলেন?
ধ্যানে। তোর পিছনে আমি একটা কালো ছায়া দেখতে পাই। বুঝতে পারি তোর বড় কোন বিপদ আসন্ন এবং সেটা এই পৃথিবীর কারও কাছ থেকে নয়। আংটির ক্ষমতা খুব সামান্য, ওটা তোকে বাঁচাতে পারত না। তাই বাধ্য হয়ে আমাকে নিজেই আসতে হলো।
আর…আর রুদ্র?
এ রুদ্র নয়, সে তো নিজের চোখেই দেখলি। তোর বন্ধু রুদ্র তিন বছর আগেই মারা গেছে। এই প্রেত তোর পিছে লেগেছিল অনেক আগে থেকে। তোর জীবনে ইদানীংকালের ভেতর যেসব বিপদ এসেছে তার সবগুলোর পিছনেই এর হাত ছিল।
ত-তার মানে? আমাকে এসব বিপদে ফেলে ওর কী লাভ?
ও আসলে আমার কাছেই আসতে চেয়েছিল। কিন্তু খুবই নিম্নস্তরের শক্তি ধরে ওর মত অশরীরীরা, আমার ধারে কাছেও যে কারণে ও ভিড়তে পারত না। এজন্যেই ও তোর সাহায্য নিয়েছিল। প্রথমে তোকে নানা বিপদে ফেলে মানসিকভাবে দুর্বল করে নেয়। তারপর রুদ্র সেজে আসে তোর কাছে। জানত আমার কথা বললে পুরানো বন্ধুর কথা তুই ফেলবি না। আংটিটা আমার কাছে আছে এটা কেউ জানত না। আমি বেশিদিন হাতে রাখতে চাইনি, কারণ অশরীরী জগতে আমার একটু বেশিই আনাগোনা। যে কেউ জেনে যেতে পারত। এই আংটিটা দেখতে খুবই সাধারণ, কিন্তু এটা হাতে পেলে ওর শক্তি বহুগুণে বেড়ে যেত। জিনিসটা মানুষের চেয়ে অশরীরীদের জন্যেই বেশি দরকারী।
কিন্তু ও যদি ভালভাবে চাইত, তা হলেই তো আমি দিয়ে দিতাম। এর জন্য এত ঝামেলার কী দরকার ছিল?
ওই যে বললাম, নিম্নস্তরের অশরীরী। মাথায় বুদ্ধিশুদ্ধি কম। আংটিটা দেখে লোভের ঠেলায় মাথা ঠিক রাখতে পারেনি, আসল চেহারা বেরিয়ে এসেছে। আর এমনিতেও ও তোকে মেরেই ফেলত।
এখন তা হলে কী হবে? অসহায় মুখে প্রশ্ন করল পাভেল।
ওরা যেহেতু জেনে গেছে এটা তোর কাছে আছে, আমার মনে হয় আংটিটা তোর কাছে রাখা আর উচিত হবে না। আমি নিয়ে যাচ্ছি। আর তোর বিপদের কারণ উদ্ঘাটিত হয়ে গেল, আশা করা যায় আর কোন বিপদে তুই পড়বি না। সুতরাং এই আংটিরও আর কোন দরকার নেই তোর। আসি। মৃদু হেসে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল জ্যোতিষী। হতভম্বের মত দরজার দিকে তাকিয়ে থাকল পাভেল।
.
শেষ চমকটা অবশ্য তখনও পাভেলের জন্য অপেক্ষা করছিল।
পরদিন সকালবেলা।
এমন ভয়ই পেয়েছিল পাভেল, শেষ পর্যন্ত একা একা নিজের বাড়িতে না থেকে পাশের আঙ্কেলের বাড়িতে গিয়ে ঘুমিয়েছিল। সাতসকালে বাড়িতে আসতেই দেখল গেটের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে দুজন লোক। সেই জ্যোতিষী! …আর…রুদ্র!
র-রুদ্র? তুই? তুই না মরে গেছিস? প্রায় ককিয়ে উঠল পাভেল।
আমি মরিনি। ভয় পাসনে। গায়ে হাত দিয়ে দেখ, আমি রক্তমাংসের মানুষ। হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল রুদ্র। এ রুদ্রর হাত স্পর্শ করে ভয় অনেকটা কাটল পাভেলের।
তা ছাড়া সকালের আলো, চারদিকে, রাস্তা দিয়ে লোকজন। চলাফেরা করছে। কাল রাতের ঘটনাগুলো কেমন অবাস্তব মনে হচ্ছিল এখন। কিন্তু…ওরা এখানে কেন? জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে জ্যোতিষীর দিকে তাকাল পাভেল।
আংটিটা কোথায়? পাভেলের চোখ তার দিকে ফিরতে জিজ্ঞেস করল জ্যোতিষী।
কোথায় মানে? আমি না ওটা কাল রাতেই আপনাকে দিয়ে দিলাম? হকচকিয়ে গেল পাভেল।
সব কথা খুলে বল। গতকাল আমার কাছ থেকে আসার পর কী কী হয়েছে সবকিছু।
জ্যোতিষীর কথা মত সব খুলে বলল পাভেল। কথা শেষ হতেই হতাশায় মাথার চুল খামচে ধরল রুদ্র। সব শেষ হয়ে গেল, গুরু! হতচ্ছাড়া প্রেতটাকে কিছুতেই আটকানো গেল না!
চল, দেখি কী করা যায়। কিছুতেই ছাড়ব না ওই শয়তানকে আমি। দৃঢ় গলায় বলল জ্যোতিষী।
দাঁড়ান, দাঁড়ান। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। বলল পাভেল।
অল্প কথায় বুঝিয়ে দিচ্ছি। জ্যোতিষী থেমে দাঁড়াল। ওই আংটিটা প্রেতজগতের অনেকেই হাতে পেতে চায়। রুদ্রর রূপ ধরে একটা প্রেত তোকে আমার কাছে পাঠিয়েছিল আংটিটা হাতানোর জন্য। তোর মুখে রুদ্রর নাম শুনেই আংটিটা আমি তোকে দিই। কিন্তু রুদ্রর রূপধারী এই প্রেত আংটিটা দখল করার আগেই আরেকটা অশরীরী, এবং এ প্রথম প্রেতের চাইতে বহুগুণে শক্তিশালী, তোর বাড়িতে পৌঁছে যায় এবং প্রথম প্রেতকে সরিয়ে আংটিটা দখল করে।
তার মানে,..তার মানে… বিশ্বাস করতে পারছে না পাভেল।
তার মানে কাল রাতে দ্বিতীয় প্রেত আমার চেহারা নিয়েই তোর বাড়িতে গিয়েছিল। তুই বিনা দ্বিধায় তাকে আংটিটা দিয়ে দিয়েছিস।
আমি সত্যিই বুঝতে পারিনি… কী বলবে বুঝতে পারল না পাভেল।
তোর কোন দোষ নেই। তুই তো আর আসল ঘটনা জানতিস না।
এবার রুদ্র মুখ খুলল। যাই হোক, দোস্ত, এবার আমরা যাই। অনেক কাজ বাকি। শয়তানটাকে ধরতেই হবে।
– হ্যাঁ, হাতে সময় বেশি নেই। তা হলে এবার তুই চোখ বন্ধ কর! পাভেলের দিকে তাকিয়ে বলল জ্যোতিশ্চন্দ্র। চোখ বুজল পাভেল।
এক…দুই…তিন!
বজ্রযোগীর প্রত্যাবর্তন – মুহম্মদ আলমগীর তৈমূর
এক
বৃন্দাবন ঘটকের সাথে পরিচয় হয়েছিল আমার এক আত্মীয়ের বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে যাওয়ার সময়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিয়ে-মুসলমানী এইসব অনুষ্ঠান আমি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি। বিয়ে বাড়িতে যতবার গিয়েছি ততবারই আনন্দের চেয়ে বেদনাই বেশি হয়েছে। এখনকার কথা বলতে পারব না, তবে আগের দিনে কোনও একটা গণ্ডগোল মন কষাকষি কিংবা দুর্ঘটনা ছাড়া বিয়ে হওয়া অসম্ভব ছিল। আমার ছোট চাচার বিয়ে হয়েছিল বছরের সবথেকে ছোট দিন ২২শে ডিসেম্বর রাতে। উনপঞ্চাশ মাইল দূরে কনের বাড়ি। সারাদিনের পথ। সকাল সাতটায় বারাত বের হওয়ার কথা ছিল। সেটা বেরুতে বেরুতে বাজল এগারোটা। দাদা হাঁপানির রোগী। ভোর বেলায় ফজরের নামাজ পড়তে উঠেছেন, এমন সময় শুরু হলো শ্বাস-কষ্ট। চোখের পাতাটাতা উল্টে বিশ্রী কাণ্ড। ওরে আমার কী হলো রে, বলে পাড়া মাথায় তুলে ফেলল দাদী। যমের জিম্মায় বাপকে রেখে কোন্ ছেলে আর বিয়ে করতে যাবে? ঘণ্টা তিনেক পর দাদা খানিকটা সুস্থ হয়ে হাঁসের মত ফ্যাসফাস করে বললেন, মেয়ের বাপকে পাকা কথা দেয়া আছে। এ বিয়ে হতেই হবে। এক্ষুণি বেরোও।
মফস্বলের বিয়ে হিটলারের প্যাঞ্জার বাহিনী না যে এক্ষুণি বেরুতে বলল আর তক্ষুণি লেফট-রাইট করতে করতে দশ প্লাটুন বেরিয়ে গেল। মেয়েরা সব কাপড়টাপড় খুলে স্নো পাউডার মুছে পানের বাটা নিয়ে বসেছে। ছেলেরা যে যার মত এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করছে। চায়ের দোকানে বসে বিড়ি-সিগারেট ফুকছে। তাদের এত কীসের গরজ! যার বিয়ে সে বুঝুক। ছোট চাচা ফুসুরফুসুর করে আমার ফুপাকে বললেন, দুলাভাই, তাড়াতাড়ি করেন। অলরেডি অনেক বেশি দেরি হয়ে গেছে। অত দূরের পথ…।
তা তো বটেই। তবে তার থেকে বড় জিনিস হলো পরীর (আমার ফুপাতো বোন) নানার যদি আবার হাঁপানির টান ওঠে, তা হলে তোর বিয়ের ফুল কুঁড়িতেই বিনাশ। নিপ ইন দ্য বাড। এদিকের লোকে বলবে, মেয়ে অলক্ষুণে, ওদিকের ওরা বলবে ছেলের বংশে হাঁপানি-পাগলামি এইসব আছে। এখানে বিয়ে দেয়া যাবে না। একবার বেরুতে পারলে হাঁপানি হোক আর হ্যাঁমারেজ, আগে বিয়ে তারপর বাড়ি ফেরা। তোর ব্যাপারটা আমি বুঝি। একদম টেনশান করিস না। দুমিনিটের ভেতর বারাত বেরুনোর ব্যবস্থা করছি। তোর বিয়ে আজকেই হবে।
পরীকে ডেকে ফুপা বললেন, এই, পরী, তোর মাকে একটু ডাক তো। এমনি এমনি ডাকছে বললে এখন কিছুতেই আসবে না। বলবি, আব্দু প্রেশারের ওষুধ খুঁজে পাচ্ছে না। আব্দুর বমি-বমি লাগছে। বলবি আমি বিছানায় শুয়ে আছি।
ফুপু এলেন প্রায় সাথে সাথে।
ফুপা বললেন, জরী, জরুরি কথা শোন, ওই চিটার কন্ট্রাকটার ঝন্টুকে তো চেনো। এই হারামজাদা আজ দুবছর হলো দুলাখ টাকা নিয়ে আজ দেব কাল দেব করছে। শেষমেষ কানা কামালকে লাগিয়েছিলাম। টাকা দিতে পারবে ঝন্টু। তবে রাস্তার ধারে ওর পাঁচ কাঠা জমি আছে। ওটা লিখে দিতে চাচ্ছে। কানা কামাল খবর পাঠিয়েছে, কালকেই ঝন্টুকে রেস্ট্রি অফিসে ধরে নিয়ে আসবে। ভাবছি, জমিটা তোমার নামে রেস্ট্রি করাব। জামিলের বিয়েটা হয়ে গেলে ওখান থেকেই বাড়ির পথে রওনা হয়ে যেতাম। যে অবস্থা দেখছি তাতে বারাত আজ বের হবে বলে তো মনে হচ্ছে না। ওদিকে কাল যদি বাড়ি না পৌঁছতে পারি, তা হলে ঝন্টুকে আবার কবে ধরতে পারব কে জানে! এরা হলো ফটকাবাজ লোক। একপোজনের কাছে টাকা ধার করে বসে আছে।
পরী বলল তোমার প্রেশার, ওষুধ খুঁজে পাচ্ছ না। দাঁড়াও, ওষুধ খুঁজে দিচ্ছি। আগে ওষুধ খাও, তারপর বিয়ের ব্যাপারটা দেখছি।
এইবার কাজ হলো কারেন্টের মত। ছোট চাচার বারাত বেরিয়ে গেল দশ মিনিটের ভেতর। এক ধ্যাড়ধ্যাড়া বাসে আমরা চৌত্রিশজন বরযাত্রী রওয়ানা হলাম। রাস্তা খানা-খন্দে ভর্তি, গাড়ি চলছে খুব ধীরে। নাটোরের বিড়ালদাহ মাজারের কাছে রাস্তা ভাল পেয়ে ড্রাইভার স্পিড উঠাল। গাড়ি চলছে। সাঁই-সাই। জানালা দিয়ে হু-হুঁ করে বাতাস ঢুকছে ভেতরে। আরামে অনেকেরই চোখ বুজে এসেছে, দুর্ঘটনাটা ঘটল ঠিক সেই সময়। কোত্থেকে একটা ছাগল এসে দৌড়ে রাস্তা পার হতে শুরু করল। ড্রাইভার ছাগল বাঁচাতে যেয়ে এক বাগানে নামিয়ে দিল বাস। সামনের চাকা হুড়মুড় করে গিয়ে পড়ল এক চৌকো গর্তে। ভাগ্য ভালই বলতে হবে, হতাহত হয়নি কেউ। কাণ্ড দেখে আশপাশ থেকে কিছু লোকজনও এসে উপস্থিত হলো। জানা গেল পরিত্যক্ত এক গোরস্থানের বহু পুরনো কবর ওটা। বয়স্ক অনেককেই বেশ চিন্তিত মনে হলো। যাত্রার প্রথম থেকেই বাধা। কবরে যানবাহন পড়ে যাওয়া বড় ধরনের কুলক্ষণ। বিপদের হাত-পা নেই, কখন কোন্ দিক থেকে আসে কে জানে! বাস কবর থেকে উঠানো হবে কীভাবে? হলেও ওটা আবার চালু হবে কিনা সেটাই বা কে বলতে পারে? কনের বাড়ি এখনও ত্রিশ মাইল পথ। ভাল মুসিবতে পড়া গেছে। মেয়েদের কেউ কেউ বাথরুমে যাওয়ার জন্যে অস্থির। স্থানীয় কিছু লোক বলল একটু দূরেই বৃন্দাবন ঘটক নামে এক প্রাইভেট কলেজের শিক্ষকের দালান বাড়ি। মহিলারা সেখানে গেলে ভালভাবে বাথরুম করতে পারবে। মেয়েরা দল বেঁধে বৃন্দাবন ঘটকের বাড়ির পথে রওনা হলো। সাথে ছোট চাচা, ফুপা আর আমি।
দুই
জানালা দরজায় খড়খড়ি লাগানো ব্রিটিশ আমলের পুরনো দোতলা বাড়ি। বাগান ও বারান্দা সব ঝকঝকে তকতকে। বোঝাই যাচ্ছে এরা বনেদি পরিবার এবং এখনও সচ্ছল। এক রামুকাকু শ্রেণীর লোক আমাদের বাইরের ঘরে বসিয়ে ভেতরে খবর দিতে গেল। কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এলেন বাড়ির মালিক বৃন্দাবন ঘটক। ধুতি-ফতুয়া পরা ছোট করে ছাটা চুল, স্বাস্থ্য একটু মোটার দিকে। তিনি আমাদের চা নাস্তা তো খাওয়ালেনই, সেই সঙ্গে একটা গাড়িরও ব্যবস্থা করে ফেললেন। ভদ্রলোক আমাদের তিনজনকে নিয়ে চা খেলেন তার পড়ার ঘরে। লক্ষ করলাম, কামরার আলমারিতে সাজানো অদ্ভুত দর্শন সেকেলে সব জিনিস। এসবের ভেতর তিনটে জিনিস দেখলে গা শিরশির করে। একটা হলো পূর্ণ বয়স্ক সক্ষম পুরুষদের অণ্ডকোষ চূর্ণ করে পুরুষত্বহীন বা খোঁজা করার যন্ত্র। আর একটি জিনিস হচ্ছে শূল। মৃত্যুদণ্ড পাওয়া আসামিকে শূলে চড়িয়ে মারা হত। কাঠের মোটা পাটাতনের সাথে নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে শক্ত করে বসানো তীক্ষ্ণ মাথাঅলা সাড়ে তিন ফুট লম্বা লোহার প্রায় তিন ইঞ্চি মোটা একটা রড। রডে ভাল করে ঘি-তেল-কলা মাখিয়ে আসামিকে তার ওপর বসিয়ে দেয়া হত। রডের চোখা মাথা আসামির গুহ্যদ্বার দিয়ে ঢুকে গলা-মুখ কিংবা চোখের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যেত। অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক বীভৎস মৃত্যু। এর তুলনায় ফাঁসি অনেক আরামদায়ক। তিন নম্বর হলো ছোট লম্বাটে একটা কোদাল। কোদালের আকৃতি এবং গঠনই বলে দিচ্ছে ওটা মাটি কোপানো সাধারণ কোদাল না। খুব কৌতূহল হলো। বৃন্দাবন ঘটককে জিজ্ঞেস করলাম, এটা তো মনে হচ্ছে কোদাল, ঠিক না?
জী, কোদালই বটে। তবে সাধারণ কোদাল না।
কিছু লোক কথা বলার সময় নাটকীয়তা খুব পছন্দ করে। বৃন্দাবন ঘটককে সেই গোত্রের লোক বলে মনে হলো। বললাম, বাবু, বিষয়টা একটু খুলে বলেন না।
ওটা ঠগীদের কোদাল। ঠগীরা মনে করত মন্ত্রপূত কোদাল শক্তির উৎস। একটা দলের কাছে কোদাল থাকত একটাই। জানেন তো একেকটা দলে কোনও কোনও সময় তিন-চারশো ঠগীও থাকত। বিশাল সব কাফেলা। মানুষ শিকারের নেশায় পথ চলছে মাসের পর মাস। এদের হাতে পুরো ভারতবর্ষে প্রতি বছর খুন হত প্রায় পঞ্চাশ হাজার পথিক। চমকে ওঠার মত ফিগারই বটে। তবে নির্ভেজাল সত্যি।
কোদাল বানাতেও অনেক তন্ত্রমন্ত্র পুজোপাঠ, নররক্ত, পশুবলির দরকার হত। সময়ও লাগত প্রচুর। তবে একবার বানানো হয়ে গেলে কোদালের থাকত অলৌকিক ক্ষমতা। এই কোদালকে কুয়োর ভেতর ফেলে দিলেও ওটা একাই উঠে আসত। যাত্রা শুরুর আগে কোদাল মাটিতে ফেলে ঠগীরা জেনে নিত কোন পথে যেতে হবে। কোন পথে পাওয়া যাবে ধনী পথিক, পথ চলতি বণিক কিংবা রাজকর্মচারী অথবা তাদের পরিবার। ঠগীদের মতন নিষ্ঠুর এবং নিপুণ খুনির দল পৃথিবীতে বিরল। এটি আমার কথা নয়, ইংরেজ ঐতিহাসিকদের কথা। ঠগীরা ছিল আমাদের মতই ঘর সংসারী, নিপাট ভদ্রলোক, কিন্তু ছদ্মবেশী এবং নিষ্ঠুরতম খুনি। যে-কোনওরকম রক্তপাত ঠগীদের জন্যে ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এরা নরহত্যা করত গলায় ফাঁস লাগিয়ে। এরপর যেভাবে লাশ গুম করত, সেটা শিল্পের পর্যায়ে পড়ে। তারা দেখিয়ে না দিলে কোনওভাবেই সে লাশ খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল না। মেয়ে-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ এদের কাছে সবই সমান। খুনের পর সামান্যতম অনুশোচনাও কখনও অনুভব করেনি। ঠগীরা। কোদাল হারিয়ে ফেললে অর্থাৎ কোদাল নিজ থেকে চলে গেলে ঠগীদের মন ভেঙে যেত। অনেক সময় ভেঙে যেত দলও। বাড়ি ফিরে যতক্ষণ না সর্দার আরেকটি কোদাল তৈরি করতে পারছে, ততক্ষণ খুনোখুনির সব কাজ বন্ধ।
এত দুষ্প্রাপ্য জিনিস আপনি পেলেন কীভাবে?
ও-কথা না-ই বা শুনলেন।
হালকা হেসে কথাটি বলেছিলেন বৃন্দাবন ঘটক।
বৃন্দাবন ঘটকের সাথে পরিচয় এভাবেই। রাস্তাঘাটে খুব বড় উপকার যারা করে, সাধারণত তাদের সাথে এ জীবনে দেখা খুব কমই হয়। হলেও সেই উপকারের এক কণাও ফেরত দেয়া হয় না কখনও। বরং উল্টো এক ধরনের অস্বস্তি হয়।
বৃন্দাবন ঘটকের সাথে আমার দ্বিতীয়বার দেখা হলো সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিবেশে।
তিন
রাজশাহীর বরেন্দ্র যাদুঘর, মধ্যযুগের পুণ্ড পাণ্ডুলিপি এবং পালি ভাষার চর্চা এই বিষয়টি নিয়ে এক জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করেছিল। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমন্ত্রিত হয়ে সেমিনারে যোগ দিয়েছিলাম আমি। যাদুঘরের অডিটোরিয়ামে দুপুর দুটোয় বরেন্দ্র অঞ্চলে পালি ভাষার প্রসারের ওপর আমার পেপার প্রেজেন্ট করার পর শুরু হলো প্রশ্নোত্তর পর্ব। কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পর ঘোষক যখন আমার প্রেজেন্টেশান শেষ হওয়ার ঘোষণা দিল, ঠিক সেই মুহূর্তে পেছনে একজন উঠে দাঁড়িয়ে গেল। তার নাকি একটা প্রশ্ন আছে। মাইক্রোফোন ততক্ষণে দর্শকদের হাত থেকে ঘোষকের হাতে ফিরে গেছে।
প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ।
আপনার প্রশ্নের জবাব দেয়ার সময় এখন আর নেই, দুঃখিত, ঘোষণা করলেন ঘোষক।
স্টেজ থেকে নেমেই পড়েছিলাম। তারপরেও ঘোষককে বললাম, আচ্ছা, ঠিক আছে। দেখা যাক ওঁর প্রশ্নটা কী।
মধ্যযুগে পুণ্ড্রনগরী অর্থাৎ বগুড়ার মহাস্থান গড়ে পালি ভাষার ব্যাপক চর্চা করতেন একজন প্রখ্যাত মহিলা। যুবতী বয়সে ইনি আত্মহত্যা করেন। বলা হয় এঁর মৃত্যুর পরপরই এ অঞ্চলে পালি ভাষার চর্চা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। আপনি এ ব্যাপারে কোনও আলোকপাত করেননি। কেন করেননি?
অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি মফস্বল শহরের এইসব সেমিনারে স্থানীয় কিছু লোক প্রায়ই উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করে দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে। এরা চায় সেমিনারের বক্তাদের উটকো ঝামেলায় ফেলে বাহবা পেতে। এদের জন্যে একটা আলাদা প্রস্তুতি রাখতে হয়। তবে স্বীকার করতেই হবে, এই বিষয়ে আমি কিছুই জানতাম না। পেপার তৈরি করেছি তাড়াহুড়ো করে। এখন বুঝতে পারছি আমার আরও পড়াশুনা করার দরকার ছিল। কিন্তু সেই স্বীকারোক্তি এখন দিলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, সেই মহিলার নাম কি শীলাদেবী?
এটা একটা চালাকি ধরনের উত্তর। মধ্যযুগের ইতিহাসে শীলাদেবী বেশ প্রচলিত নাম। ভদ্রলোক যদি বলেন হ্যাঁ তা হলে বলব এটি অত্যন্ত বিতর্কিত বিষয়। এই ব্যাপারে ঐতিহাসিকরা কেউই একমত হতে পারেননি। ওটাকে কিংবদন্তি ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। আর ভদ্রলোক যদি বলেন না তা হলে বলব আপনি কোন মহিলার কথা বলছেন বুঝতে পারছি না। ইতিহাসে তো শুধু শীলাদেবীর উল্লেখ আছে। তবে তার অবদান তেমন বিশেষ কিছু নয়।
ভদ্রলোকের উত্তর হলো হ্যাঁ বাচক এবং আমিও হা-এর উত্তরে যা বলার তাই-ই বললাম। লক্ষ করলাম, উত্তর শুনে ভদ্রলোক সামান্য হাসলেন। অন্যান্য মফস্বলী পণ্ডিতদের মত তর্ক না জুড়ে বসে পড়লেন। বিকেল পাঁচটায় সেমিনার শেষ করে অডিটোরিয়াম থেকে আমরা সবাই বের হচ্ছি, হঠাৎ শুনতে পেলাম কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছে। ঘুরে তাকাতেই দেখলাম পঞ্চাশোর্ধ্ব এক হিন্দু ভদ্রলোক দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। সেই প্রশ্নকর্তা। দেখে যেন মনে হয়: চিনি উহারে। এর আগেও এঁকে কোথাও দেখেছি। লোকটির কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি পেছন থেকে ডাকছিলেন আমাকে?
জী, আমিই ডেকেছি।
আপনাকে চেনা চেনা লাগছে। আগে আপনার সাথে দেখা হয়েছে কখনও?
জী, তা একবার হয়েছে। আজ থেকে আট-দশ বছর আগে যখন আমার বাড়িতে এসেছিলেন, তখন দেখা হয়েছে।
ঠিক বুঝলাম না। খুব পরিচিত দুএকজন ছাড়া কারও বাড়িতে আমি কখনও যাই না। আপনার বাড়ি কোথায়? আর গিয়েইছিলাম বা কী কারণে-বলতে পারবেন?
আমার ধারণা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরদের স্মরণশক্তি প্রখর হয়। যা হোক, আমার বাড়ি নাটোরের বিড়ালদাহ মাজারের কাছে। আপনাদের কোনও এক আত্মীয়ের বিয়ে ছিল। আপনারা আমার বাসায় কিছু সময়ের জন্যে অতিথি হয়েছিলেন। আমার নাম বৃন্দাবন ঘটক এরপরও যদি চিনতে না পারেন, তো আর কিছু করার নেই।
আমার সবকিছু মনে পড়ল, কিছুটা লজ্জাও পেলাম। এঁর কথা ভুলে যাওয়া খুবই অন্যায় হয়েছে। তার হাত ধরে বললাম, বাবু, আপনাকে চিনতে না পারার জন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। প্লিজ, কিছু মনে করবেন না।
আরে না। এরকম হয়। আসুন, কোথাও গিয়ে একটা বসি। আপনাদের এখন অন্য কোনও প্রোগ্রাম নেই তো?
আজ সন্ধ্যায় ঘোড়ামারায় একটা ভাল হোটেলে আয়োজকরা আমন্ত্রিতদের সম্মানে ডিনারের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু সেকথা বৃন্দাবন ঘটককে আর বললাম না।
না। তেমন কিছু নেই। সন্ধেটা ফ্রি আছি। কোথাও যেতে ইচ্ছে হলে চলেন। মন খুলে কথা বলা যাবে।
পদ্মার পাড়ে বিকেলে হাঁটতে ভাল লাগে। চলুন। ওদিকটাতে যাই।
কোনও সমস্যা নেই। আপনি যেখানে ভাল মনে করেন।
চার
রাজশাহী শহরে পদ্মার ধার ঘেঁষে অনেক উঁচু আর বিশাল লম্বা বাঁধ দেয়া হয়েছে। বৃন্দাবন বাবু আমাকে নিয়ে বাঁধের ওপর উঠে হাঁটতে লাগলেন। সবথেকে ভাল লাগল ব্রিটিশ আমলের বড় বড় অফিসারদের বাড়িগুলো যেখানে, সেই জায়গাটা। পদ্মার ধারে লাইন দিয়ে প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডঅলা লাল রঙের বড় বড় সব বাড়ি। দরজার সমান বড় অসংখ্য জানালা তাতে। কোথায় বাড়ি করতে হবে সেটা ইংরেজদের চেয়ে ভাল আর কেউ জানত না। হাত-পা ছড়িয়ে বাঁধের ওপর বসলাম আমরা। এক বাদামঅলাকে ডেকে দুছটাক বাদাম কিনলেন বাবু। বললেন, আসুন, খেতে খেতে গল্প করি।
এইসব বাড়িগুলোতে কারা থাকে এখন?
ডিসি, এসপি, বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার এইসব লোকেরা। ইংরেজ সাহেবদের চেয়েও এদের ঠমক বেশি। দেশের সব ভাল ভাল জিনিস এরাই ভোগ করে। সাধারণ মানুষ আগে ইংরেজদের গোলামি করত, এখন করে এদের দাসত্ব। যেই লাউ সেই কদু।
এ হচ্ছে জর্জ অরওয়েলের দি এনিমেল ফার্ম। সিস্টেম একই থাকে, শুধু তোক পাল্টে যায়। ধনতন্ত্র অবিনাশী।
আগে কিন্তু এরকম ছিল না। রাজনৈতিক পট পরিবর্তন হলে সবকিছু পাল্টে যেত। এই পুরাজ্যের কথাই ধরেন।
বাবু, আপনি পালি ভাষার বিষয়ে অনেক জানেন বলে মনে হচ্ছে। পুরনো জিনিসের মত পুরনো ভাষাতেও আপনার আগ্রহ আছে নাকি? : আগ্রহ ছিল না। তবে বিশেষ কারণে আগ্রহ হয়েছে। আপনার কখনও যাকে বলে অতিপ্রাকৃত এমন কোনও
অভিজ্ঞতা হয়েছে?
জী-না। আমি মানুষ হয়েছি শহরে। আমার ধারণা, অতিপ্রাকৃত ঘটনা শহরের চেয়ে গ্রামেই বেশি ঘটে। প্রাকৃত অপ্রাকৃত কোনও ঘটনা নিয়েই শহরের মানুষের মাথা ঘামানোর সময় নেই। যান্ত্রিকতা এবং ভৌতিকতা দুই মেরুর জিনিস।
এ কথা ঠিক না। শহরেও অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটে। তবে সেটা জানাজানি হয় কম। যা হোক, আমার জীবনের একটা ঘটনা আপনাকে বলি। একদম সত্যি ঘটনা। তখন জানুয়ারির শেষ। আমি বিড়ালদাহ হাইস্কুলে মাত্র ক্লাস সিক্সে উঠেছি। স্কুল থেকে সিদ্ধান্ত হলো সেবছর বার্ষিক পিকনিক হবে নাটোরের রানী ভবানীর প্রাসাদে। চাল, ডাল, মশলা, ছাগল, তেল, হাঁড়ি-পাতিল, থাল, বাটি এসব নিয়ে শিক্ষক-ছাত্র কেরানী-পিওন ঠাসাঠাসি করে দুটো বাসে রওনা হলো। ভোরে বাস ছাড়ার পর সবাইকে কাগজের ঠোঙায় দেয়া হলো মুড়ি ও পাটালিগুড়ের নাস্তা। সেযুগে বোতলের পানি ছিল না। একজগ পানির সবটাই স্যররা খেলেন। আমরা এক বুক তৃষ্ণা নিয়ে বসে থাকলাম কখন রানী ভবানীর প্রাসাদে পৌঁছব, সেই আশায়। প্রাসাদে পৌঁছে টিউবওয়েল থেকে পেট ভরে পানি খেলাম সবাই। তারপরই ঘটল বিপত্তি। ভোরে উঠে অনেকেই বাথরুম করার সময় পায়নি। দেখা গেল ওই কাজ এখন সমাধা না করলেই নয়। এত বাথরুম তো সেখানে নেই। ঝোঁপঝাড়ই ভরসা। আমি যেখানেই যাই, সেখানেই কেউ না কেউ বসে পেট খালি করছে।
হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম কম্পাউণ্ডের সর্ব দক্ষিণ কোণে। চারদিকে আম-কাঁঠালের বাগান। এরই আড়ালে জবুথুবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তিনদিকে টানা বারান্দাঅলা মন্দির। ধরনের প্রাচীন এক দালান। ছাদ ধসে পড়েছে, কয়েকটা থামে ভর দিয়ে দেয়াল তখনও খাড়া হয়ে আছে বটে, তবে ওগুলো ছেয়ে গেছে বট আর অশ্বত্থ গাছের শেকড়ে। লাল রঙের মেঝে এখনও যথেষ্ট উঁচু। একটাই ঘর, তবে ভেতরে ঢোকার পথ তিনটে। দেয়ালের সাথে ফিট করা লোহার ক্ল্যাম্প দেখে বোঝা যায়, আগে ওগুলোতে দরজা ছিল। ফেটে চৌচির সিঁড়ি বেয়ে উঠে ভেতরে উঁকি দিলাম। ঘরের মেঝে গাছের মরাপাতা, ভাঙা ইটের টুকরো ও ধুলোবালিতে বোঝাই। হঠাৎ চোখে পড়ল লাল-সাদা পাথরের মেঝের এককোণে কালো রঙের স্বস্তিকা আঁকা। স্বস্তিকার চার বাহুতে থেবড়ে বসে আছে হিন্দু ধর্মের চার প্রধান দেবদেবী। এদের চারজনের মাথার ওপর চার পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে এক গাভী। তার পিঠের ওপর কৃষ্ণের কাটা মাথা হাতে বসে আছে মহিষাসুর। পুরো চিত্রটা ছয়কোনা একটা লাল তারার ভেতর আঁকা।
হঠাৎ ওই বৃত্তটা থেকে বাতাসের ছোট্ট একটা ঘূর্ণি উঠল। শুকনো পাতা, ধুলোবালি, পাখির পালক ঘুরপাক খেতে লাগল ঘূর্ণির ভেতর। আস্তে আস্তে একটি মানুষের আকৃতি পেল ঘূর্ণিটা। লালচর্মসর্বস্ব এক বুড়ো। গায়ে কোনও কাপড়চোপড় নেই। মাথায় জট পাকানো চুল, নীলচে লম্বা দাড়ি, হলদেটে চামড়া। দেখলাম সম্পূর্ণ নগ্ন ওই বুড়ো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বুড়োর দৃষ্টি থেকে চোখ ফেরাতে পারছি না। এক ঘোরলাগা অবস্থা হলো। বারান্দা পেরিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে যেতে লাগলাম দরজার দিকে। যেতেই হবে ওই ন্যাংটো বুড়োর কাছে। চৌকাঠ পেরিয়ে ঘরের ভেতর পা রাখব, এমন সময় মেয়েলী গলায় পেছন থেকে কে যেন ডাকল আমাকে। ঘোর কেটে গেল। তৎক্ষণাৎ। ঝট করে পেছনে তাকালাম। কোথাও কেউ নেই। দূরে শিমুল গাছের ডালে বসে একটা ঘুঘু ডাকছে। জীবনে কখনও এত ভয় পাইনি। লাফিয়ে নেমে এলাম বারান্দা থেকে। পেছন ফিরে আর তাকানোর সাহস হয়নি।
এক দৌড়ে প্রাসাদের সামনে এসে দেখি জলিল স্যর সবাইকে একটা করে টোস্ট বিস্কুট দিচ্ছেন। এই স্যর সমাজ, বিজ্ঞান, বাংলা এইসব ক্লাস নেন। ইনি ক্লাসে কিছু পড়ান না, শুধু পড়া ধরেন। প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে পিঠের ছাল চামড়া সব তুলে ফেলেন। একবার বাংলা ব্ল কবিতা যাকে আমরা বলতাম ছিপখান তিন দাঁড় পুরোটা মুখস্থ বলতে না পারায় আমাকে এত জোরে চড় মারলেন যে তিন দিন ধরে কানের ভেতর ঝিঁঝি পোকা ডেকে গেল। আমার তখন বুক কাঁপছে। তারপরও দুরমুশ জলিলের (স্কুলের ছেলেরা স্যরকে এই নামেই ডাকত) কাছ থেকে বিস্কুট নিলাম। বিস্কুট খেয়ে আমরা সবাই আরও এক রাউণ্ড পানি খেলাম। এর পরপরই পেট নেমে গেল আমার। দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে শুয়ে পড়লাম গাছের নিচে। আমার অবস্থা দেখে খেপে গেলেন জলিল স্যর।
সবাইকে শুনিয়ে বললেন, এইসব উটকো ঝামেলা তার একেবারে পছন্দ না। ক্লাস টেনের এক ছাত্রকে দিয়ে লোকাল বাসে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন আমাকে। আমাদের পাড়ারই ছেলে। তার আর পিকনিক খাওয়া হলো না। এরপর একমাস কালাজ্বরে ভুগলাম। ঘুমালেই হলদেটে ঝুলঝুল চামড়ার এক কুৎসিত নগ্ন বুড়োকে দেখতে পেতাম। সন্ধের পর একা থাকতে ভয় করত।
উনি থামতেই আমি বললাম, বৃন্দাবন বাবু, আপনি এটাকে অতিপ্রাকৃত ঘটনা কেন বলছেন? ওটা একটা হ্যালুসিনেশান। এই কাহিনির সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো ওই নগ্ন বুড়ো। সবদেশেই ভয়ানক বিকৃত রুচির কিছু বুড়ো থাকে। এরা শিশুদের সাথে নানারকম নোংরা কাজকর্ম করে। যৌন বিষয়ে শিশুদের কোনও ধারণা থাকে না। তাদের কচি মনে গভীর ছাপ ফেলে এইসব জঘন্য কর্মকাণ্ড। একটা ঘটনা বলি। ক্লাস নাইনে উঠে আমরা আগের বছরের ফেল করা এক ছাত্রকে পেলাম। প্রত্যেক ক্লাসেই এরকম একজন দুজন থাকে। তবে এর ব্যাপার আলাদা। এই ছেলেকে দিয়ে তাদের পাড়ার এক বুড়ো পায়ু মৈথুন করাত। বারংবার এই ঘটনা ঘটার পর তীব্র অপরাধবোধে ভুগতে শুরু করে ছেলেটি। পরে বহুদিন ঘরে আটকে রেখে তার মানসিক চিকিৎসা করাতে হয়েছিল। হয়তো ছোটবেলায় আপনিও ভিকটিম হয়েছিলেন।
জী-না। একমাত্র সন্তান হিসেবে আমি বড় হয়েছি কঠিন বেষ্টনীর ভেতর। বাড়িতে মা সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখতেন। বাইরে বের হলে সাথে বয়সে বড় কেউ না কেউ থাকতই। তবে এর পরের ঘটনাগুলো শুনলে আপনার কাছে। বিষয়টি আরও স্বচ্ছ হবে।
পরে আবার কী ঘটনা ঘটল, সে বুড়োর পরিচয় জানতে পারলেন?
সত্যি কথা বলতে কী, ব্যাপার কিছুটা সেই রকমই। এক বছর পরের ঘটনা। আমি তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। সেই সমগ্ন গরমের ছুটিতে মা আমাকে নিয়ে বেড়াতে গেলেন নানাবাড়ি রামপুর বোয়ালিয়ায়। রাজশাহী-বগুড়ার মাঝখানে এক প্রত্যন্ত অঞ্চল এটি। প্রত্যন্ত অঞ্চল হলেও খুব বিখ্যাত। সন্ধের সময় অভ্যেসমত মায়ের আঁচল ধরে বসে আছি দেখে বড় মামা মাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী রে, রমা, বিনু এত ভয় পাচ্ছে কেন?
মামাকে ভেঙেচুরে সবকিছু জানালেন মা।
তখন মামা বললেন, সিধু জ্যাঠার কাছে নিয়ে যাব কালকে। দেখি উনি কী বলেন৷
পাঁচ
পরদিন বিকেলের দিকে বড় মামা আমাকে সিধু জ্যাঠার কাছে নিয়ে গেলেন। ওই এলাকায় সবচেয়ে পুরনো আর বড় বংশই মামাদের বংশ। এই সিধু জ্যাঠা আমার নানার ভাই। ইনি দিনে করেন কবিরাজি আর রাতে মহাকালদেবীর পুজো। গাঁয়ের লোকেরা তাঁকে মনে করে তান্ত্রিক। ভাল জ্যোতিষী হিসেবে নাম-ডাক আছে। মন্দিরের কাছাকাছি সেবায়েতের যে পোড়ো বাড়ি ছিল, সেই বাড়িরই ভিটের ওপর বাড়ি করেছিলেন সিধু জ্যাঠার পরদাদা। সেই বাড়িও বলতে গেলে অনেক আগের। জ্যাঠা বিয়ে-শাদি করেননি। তার এক বাল্যবিধবা বোনকে নিয়ে একাই থাকেন ওই জড়ভরত বাড়িটাতে। দেখলাম জ্যাঠার পরনে লালসালু। লম্বা দাড়ি, কাঁচাপাকা চুল মাথার ওপর চুড়ো করে বাঁধা। কপালের মাঝখানে রক্ত তিলক। রাত জেগে জেগে চোখ লাল। পোচ। পোঁচ কালি জমেছে চোখের নিচে। সম্পূর্ণ অনুভূতিশূন্য মরা মাছের চোখ। ওগুলোর দিকে তাকালে ধড়াস করে ওঠে বুকের ভেতর। ঘরের দাওয়ায় মাদুরে বসে ঝকঝকে কাঁসার বাটিতে নারকেল কোরা দিয়ে গুড়মুড়ি খাচ্ছেন সিধু জ্যাঠা। বড় মামাকে দেখে বললেন, বনস্পতি যে, তা এদিকে কী মনে করে?
জ্যাঠা, এ হলো রমার ছেলে বৃন্দাবন। বিড়ালদাহ থেকে কালই এখানে এসেছে। ভাবলাম আপনার কাছে নিয়ে আসি।
সিধু জ্যাঠা তাঁর ইলিশ মাছের চোখ দিয়ে দেখলেন আমাকে। বললেন, আয়, মাদুরে বোস। দেখি তোর বাঁ হাত।
ঠাণ্ডা নরম হাত দিয়ে আমার বাঁ হাতের তালু মেলে ধরলেন। কিছুক্ষণ পর বললেন, কী, ছেলে, রাতে ভয় লাগে? ন্যাংটা বুড়োর কথা মনে পড়ে?
মামা কিছু বুঝলেন না, তবে আমার গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল। এ লোক অন্তর্যামী নাকি? বড় মামাকে কাছে ডেকে বললেন, বনস্পতি, এই দেখ তোর ভাগ্নের হাত দেখ। এর তো তেনার দর্শন হয়েছে রে।
কার দর্শন হয়েছে, জ্যাঠা? হাতেই বা কী দেখলেন?
তোর ভাগ্নে, এই বেন্দাবন জন্মেছে এক বিশেষ তিথিতে। তই তো কিছুই শিখলি না। সারাজীবন শুধ স্লেচ্ছদের গোলামি করলি। এর বাঁ হাতের তালুর দিকে চেয়ে দেখ। চন্দ্রের ক্ষেত্র থেকে ওই যে রেখাটা উঠে মঙ্গলের কাছে। ধনুকের মত বাঁক নিয়ে বুধের নিচে গিয়ে থেমে গেছে। অতি বিরল রেখা এটি। জাতকের হাতে এই বিশেষ রেখাঁটি থাকলে অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার অধিকারী হয় সে। বরেন্দ্রের সবচেয়ে বড় তান্ত্রিক হলো রানী ভবানীর ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা রাজা সূর্য নারায়ণ। বহুকাল আগের কথা। সে-ই সব তান্ত্রিকের গুরু। এই রেখা তার হাতে ছিল। এরই সাথে দেখা হয়েছে তোর ভাগ্নের। আর সেই থেকেই ভয়ে সিঁটিয়ে আছে বেন্দাবন। আমার কাছে এসে যখন পড়েছেই, ভয় ভাঙিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করছি। পরশু শুক্লপক্ষের নবমী। সারাদিন উপোস করিয়ে রাখবি তোর ভাগ্নেকে। সন্ধ্যায় ওকে স্নান করিয়ে মন্দিরে নিয়ে আসবি। ভয়কে পেঁদিয়ে বৃন্দাবন দেখিয়ে দেব।
সিধু জ্যাঠা ছিলেন ভয়ানক মুসলমান বিদ্বেষী। যদিও তাঁর রোগী বেশিরভাগই ছিল ওই গোত্রের লোকেরাই। চড়া ফি আদায় করতেন তাদের কাছ থেকে। লোকে বলত জ্যাঠা সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। উনি যা দাবি করতেন লোকে তাই-ই দিত তাকে।
ছয়
জ্যাঠার কথামত সন্ধের সময় বড় মামা আমাকে মন্দিরে নিয়ে গেলেন। মহাকালদেবীর মন্দির অনেক পুরনো। বহুকাল আগে বিরাট বড় ছিল। এখন শুধু অজস্র ভাঙা দেয়াল পিলারের ভেতর ছোট্ট একটি ঘরই টিকে আছে। সিধু জ্যাঠাই কোনওরকমে টিকিয়ে রেখেছেন। মহাকালদেবীর মূর্তি মন্দিরের যে ঘরটিতে ছিল সেটি বহু আগেই জরাজীর্ণ হয়ে ভেঙে পড়েছে। এর সাথে গেছে আরও অসংখ্য কামরা আর প্রকোষ্ঠ। এখন শুধুমাত্র দাঁড়িয়ে আছে মহাকালদেবীর মূর্তি যে ঘরখানাতে ছিল, তার পেছনের কামরাটি। সিধু জ্যাঠা সাধনা করেন ওই কামরাটিতেই। এটি তার কাছে খুবই পবিত্র এক সাধন পীঠ। কালো কষ্টি পাথরে তৈরি তিন ফুট লম্বা মহাকালদেবীর মূর্তি। চোখ ফেরানো যায় না এত সুন্দর। তবে এর ভেতরে কোথায় যেন ভয়ঙ্কর এক নিষ্ঠুরতা লুকিয়ে আছে। সাদা একটা থান পরিয়ে মূর্তির সামনে চিৎ করে শোয়ালেন আমাকে সিধু জ্যাঠা। আমার মাথাটা রাখলেন মূর্তির পায়ের কাছে। চোখ মেলে তাকাতেই দেখলাম দৈবী সরাসরি তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। জ্যাঠা বললেন, ভয় পাসনে, বেন্দাবন। চোখ বন্ধ করে খুব আস্তে আস্তে শ্বাস নে। মুখটা একটু হাঁ কর, দুচামচ ওষুধ খাওয়াব তোকে।
ভীষণ তেতো কী একটা খাওয়ালেন আমাকে জ্যাঠা। কিছুক্ষণ পর মনে হলো আস্তে আস্তে খুব গভীর কোনও গর্তে পড়ে যাচ্ছি। হঠাৎ দেখলাম আলো ঝলমলে একটা সবুজ ঘাসে ঢাকা উপত্যকায় দাঁড়িয়ে আছি। সামান্য দূরে ছোটখাট একটা পাহাড়ের চূড়ায় লাল আর সোনালি রঙের অপূর্ব এক বৌদ্ধ মন্দির। বিকেলের আলোয় চকচক করছে। পেছনে সাদা ধপধপে বরফে ঢাকা হিমালয়ের অসংখ্য পাহাড়-চুড়ো। বরফে রোদ লেগে রংধনুর সাত রং বেরুচ্ছে। ঢং-ঢং করে ঘণ্টা বাজতে লাগল মন্দিরটাতে। মন্দিরের সিঁড়িতে পা রাখব, এমন সময় খানিকটা দূরে একটা পাহাড়ের গুহা থেকে গলগলিয়ে ধোয়া বেরিয়ে আসতে দেখলাম। লক্ষ করলাম, ধোঁয়াগুলো আকাশে উঠতে উঠতে পৌরাণিক গল্প উপকথার বীভৎস সব প্রাণীর আকৃতি নিচ্ছে। খুব কৌতূহল হলো। কী হচ্ছে ওখানটাতে? গুহার কাছাকাছি যেতেই ধূপ এবং পোড়া ঘিয়ের গন্ধ পেলাম। গুহাটা সুড়ঙ্গের মত সামনে এগিয়ে ডানে। বাঁক নিয়েছে। বাঁকের কাছেই আলো ছড়াচ্ছে একটা জ্বলন্ত মশাল। চারদিক ঝকঝকে তকতকে। বাঁক ঘুরে দেখলাম গম্বুজের মত ছাদঅলা গোলাকার বিরাট এক হলঘরের মত। হলঘরের এখানে সেখানে পুড়ছে আরও অনেক মশাল। সামনেই গুহার দেয়াল কুঁদে বানানো চওড়া ধূসর বেদীর ওপর কালো কুচকুচে পাথরের বড় একটা মূর্তি। লাল চুনি পাথরের চোখ, কোঁকড়ানো চুল, চওড়া কপাল, পাকানো শরীর। পাতলা ঠোঁটে তাচ্ছিল্যের হাসি। মূর্তিটি অসম্ভব জীবন্ত।
বেদীর সামনে মেঝের ওপর গোল বৃত্তের ভেতর ছয়কোনা একটা তারা আঁকা। তার ওপর পদ্মাসনে বসে হোমের আগুন জ্বেলে, মন্ত্র উচ্চারণ করছে এক বৃদ্ধ। কোমরের ওপর থেকে গা খালি। মশালের আলোয় চকচক করছে শরীরের ফর্সা চামড়া। নিখুঁত কামানো মাথা, শরীরের কোথাও একটা লোম পর্যন্ত নেই। বিচিত্র এক ভাষায় গম্ভীর স্বরে অনর্গল মন্ত্র পাঠ করছে বুড়ো। মনে হলো গভীর রাতে ধানশ্রী রাগে বাঁশি বাজছে দূরে কোথাও। একটা ঘোরের ভেতর চলে গেলাম আমি। পুরোহিত আর বেদীর মাঝখানে জল ভর্তি সবুজ পাথরের শবাধারে একটি নগ্ন তরুণীর লাশ ভেসে থাকতে দেখলাম। পুরোহিতের বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে সাদা থান পরা এক যুবতাঁকেও মন্ত্র উচ্চারণ করতে দেখলাম। মেয়েটির কোমর অবধি কোঁকড়ানো এলোচল। ধপধপে সাদা সুডৌল বাহু, গোলগাল পায়ের গোছা। ছোট্ট পাতলা দুটো পাতায় সরু নিপুণ আঙুল। গোলাপি নখ ডেবে আছে সাদা তুলতুলে মাংসের ভেতর। মেয়েটির চুলের প্রান্ত বেয়ে এক ফোঁটা দুফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ে নিতম্বের কাছে কাপড় ভিজিয়ে ফেলেছে। কিছুক্ষণ আগেই স্নান করেছে বোধহয়। বুকের কাছে দুহাত জড় করে গভীর মনোযোগ দিয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করছে সে। মেয়েটিকে অসাধারণ সুন্দরী বললেও কম বলা হয়। এমন একটি মেয়ের সাথে সারাজীবনে অনেকের একবারও দেখা হয় না। মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হলো এ সাক্ষাৎ স্বরস্বতী। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে তান্ত্রিকের ডান পাশে বসে পড়লাম।
ওই সন্ন্যাসী আমাকে কিছুই বলেনি, তবুও বুঝতে পারলাম, এ বৈশালী নগরের রাজ পুরোহিত চিত্রকূট। যুবতী বৈশালী রাজকন্যা সঙ্মিত্রা। মূর্তিটি আদি পিশাচ দেবতা আহুরার। মন্ত্র পড়তে পড়তে হঠাই চিত্রকূট আমার বা হাতটা ধরল। মেঝেতে আঁকা তারার মত কাঠের একটি তারা আমার হাতের তালুতে রেখে হাতের মুঠো বন্ধ করল। ঠিক তখন সঙ্মিত্রাকে আটটি কস্তুরী মৃগনাভী, একদলা কর্পূর হোমের আগুনে নিক্ষেপ করতে দেখলাম। হোমের আগুন তৈরি হয়েছে চন্দন কাঠ দিয়ে। চারদিকের বাতাসে চন্দন পোড়ার মিষ্টি সুবাস। চিত্রকূট এবং সঙ্মিত্রার মন্ত্র উচ্চারণের শব্দ এখন চাপা ও গম্ভীর। লক্ষ করলাম, সবুজ শবাধারের ভেতরকার তরুণীর লাশটি সটান দাঁড়িয়ে গেল। পানিতে ভিজে ভিজে ওটার শরীরের চামড়া নীলচে হয়ে গেছে। পেছন দিকে বেঁকে গেল লাশটার মাথা, খুলে হাঁ হয়ে গেল মুখ। খোলা মুখ থেকে ঝলকে ঝলকে বেরুতে লাগল তীব্র আলোর রশ্মি। গম্বুজ ভেদ করে অনন্ত নক্ষত্রবীথি স্পর্শ করল সেই আলোর শিখা। একই সাথে লাশের শরীর থেকে নীলচে আলোর ঢেউ বেরিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে গেল পুরো গুহা। এরই ভেতর দেখলাম জীবন্ত হয়ে উঠেছে আহুরার মূর্তি। • আগুন-গরম ইস্পাতের মত জ্বলজ্বল করছে, চুনির চোখ। একতাল আঁধার হয়ে বেদী থেকে নেমে এল পিশাচ দেবতা। বজ্রপাতের গুমগুম শব্দে গুহার দেয়াল কাঁপতে লাগল থরথর করে। সেই জমাট বাঁধা অন্ধকার এগিয়ে এসে চিত্রকূটের দেহ ভেদ করে গম্বুজের চূড়াকে দুভাগ করে মিলিয়ে গেল আকাশে। চারদিক থেকে ভেসে এল কানে তালা ফাটানো হা হা, হা-হা, হা-হা শব্দ। তরুণীর লাশ শবাধারের পানি সব উধাও। ছয়কোনা তারাটির মাঝে পড়ে আছে চিত্রকূটের পরিধেয় সাদা কাপড়। অদৃশ্য থেকে কে যেন বলল, ভয় পেয়ো না। এখন থেকে আমাকে সবসময় কাছে পাবে তুমি।
দীর্ঘক্ষণ কথা বলে থামলেন বৃন্দাবন ঘটক।
আমি বললাম, বৃন্দাবন বাবু, এই ঘটনা থেকে আপনি আসলে কী প্রমাণ করতে চাইছেন? এখানে অতিপ্রাকৃত কোনও কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না। মেক্সিকোর অ্যাজটেকরা বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে পেয়োটি নামের এক জাতীয় ক্যাকটাস সেবন করত। সাংঘাতিক হ্যালুসিনেটরী ড্রাগ এটি। আপনার সিধু জ্যাঠা কবিরাজ মানুষ। তিনি এ জাতীয় কোনও কিছুর রস খাইয়ে থাকবেন আপনাকে।
এই ঘটনার পর কোনওদিনই কিন্তু আমি আর ভয় পাইনি।
না পাওয়াই স্বাভাবিক। ভয় সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার। আপনাকে সম্মোহিত করে স্ট্রং সাজেশান দিয়েছিলেন। আপনার সিধু জ্যাঠা। পুনরায় ভয় পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।
এ কথার কোনও জবাব না দিয়ে বৃন্দাবন বাবু তাঁর বা হাতটি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। চেয়ে দেখলাম তাঁর হাতের তালুর ঠিক মাঝখানে গাঢ় লাল রঙের ছয়কোনা একটি তারার ছাপ আঁকা। যেন ওখানটাতে উল্কি করিয়েছেন। যে বিষয়টিতে আমার সবচেয়ে বেশি খটকা লাগল, সেটি হলো তারার ছয়টি কোণ। আধুনিক তারা সবই পাঁচকোনা। ছয়কোনা তারা ব্যবহার হত সহস্র বছর আগে। কেউ যদি এর হাতে ট্যাটুও করে থাকে, তা হলে ওই তারা পাঁচকোনা হওয়ার কথা, ছয়কোনা কোনওভাবেই নয়। আমি বললাম, বাবু, সবই না হয় বুঝলাম। কিন্তু প্রশ্ন একটা থেকেও গেল। সেটি হলো এসবের সাথে পালি ভাষার সম্পর্কটা আসলে কোথায়?
ওই ব্যাপারটি জানতে হলে আপনাকে আরও কিছুক্ষণ ধৈর্য ধরতে হবে। এই রাম কাহিনি এখনও শেষ হয়নি।
হাতঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম রাত সাড়ে আটটা বাজে। প্রায় তিন ঘণ্টা হলো বাঁধের ওপর বসে আছি। নদীর জোরালো হাওয়ায় ভিজে ভিজে লাগছে শরীর, খিদেও পেয়েছে খুব। হিলহিলে ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। মনে হয় কেঁপে বৃষ্টি আসবে। বৃন্দাবন ঘটককে বললাম, বাবু, চলেন মিউজিয়ামের গেস্ট হাউসে যাই। ওখানে বাবুর্চি আছে। তাদেরকে বললেই খাবার রান্না করে দেবে। আজকে রাতে আমার সাথে খাওয়া-দাওয়া করেন।
ভেবেছিলাম বৃন্দাবন ঘটক রাজি হবেন না। কিন্তু বাস্তবে উল্টোটা ঘটল। বাবু আমার সাথে যাওয়ার জন্যে রাজি হয়ে। গেলেন। গেস্ট হাউসে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত সাড়ে নটা বাজল। আমার সাথে যারা ছিলেন, তারা সবাই ডিনারে। বাবুর্চিও রান্নাঘর সাফসুতরো করে তালাটালা দিয়ে বাড়ি যাওয়ার জন্যে রেডি। তার হাতে দেড়শো টাকা দিয়ে। বললাম, মুরগির ঝোল সরু চালের ভাত-ডাল আর ভাজি করার জন্যে। আরও বললাম, যদি খুশি করতে পারো, তা হলে আরও বিশ টাকা বখশিশ পাবে। সে সময়ে দেড়শো টাকা বেশ ভাল টাকা। বাবুর্চি বেশ চালাক-চতুর লোক। রান্নায় বসার আগেই আমাদের দুকাপ চা দিয়ে গেল। একটা পুরনো বাংলা টাইপের বাড়িকে গেস্ট হাউস বানানো হয়েছে। চা নিয়ে বেতের চেয়ার পেতে আমরা দুজন বারান্দায় বসলাম। আকাশে মেঘের ঘনঘটা, কড়কড় করে বাজ পড়ল কাছেই কোথাও। সেই সাথে চলে গেল কারেন্ট, শুরু হলো দমকা বাতাস। একই সঙ্গে বাংলোর টিনের চালে বড় বড় ফোঁটায় চড়চড় শব্দে বৃষ্টি পড়তে লাগল। নিকষ কালো অন্ধকারে ডুবে গেলাম আমরা। বৃন্দাবন বাবু আবার তার কাহিনি শুরু করলেন। তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছে না, শুধু গলা শুনতে পাচ্ছি।
সাত
এই ঘটনার পর সিধু জ্যাঠার সাথে আমার ভাব হয়ে গেল খুব। প্রতিদিন বিকেলে যাই তাঁর কাছে। নানান গল্প কাহিনি শোনান জ্যাঠা আমাকে। একদিন শোনালেন রামপুর বোয়ালিয়ার ঘটনা। বললেন, তুই জানিস না, বেন্দাবন। এই রামপুর বোয়ালিয়া এক পুরনো জনপদ। এর ইতিহাসে ঘটনার ঘনঘটা। বারোশো সালের শেষের দিকে এদেশে মুসলমান দরবেশরা দলে দলে আসতে শুরু করে। শাহ তুরকান নামের এক আউলিয়া এখানে এসে ইসলাম প্রচার করতে শুরু করলেন। সেই সময়ে এই এলাকা শাসন করত। তান্ত্রিক রাজা অংশুদেব চওবন্দী আর তাঁর ভাই খের্জুরচণ্ড। এরা পুজো করত মহাকালদেবী নামে এক জাগ্রত প্রতিমার। এই দেবীকে তুষ্ট করার জন্যে তান্ত্রিক রাজারা ফি বছর তাঁর বেদীতে নারী ও শিশু বলি দিত। এই রাজাদের সাথে তুরকান। শাহর যুদ্ধ বাধল। তুরকান শাহর পক্ষে থাকল অন্যান্য দরবেশ, অসংখ্য অনুসারী। তান্ত্রিক রাজাদের সৈন্যরা প্রথমে হেরেই যাচ্ছিল। খবর পেয়ে তান্ত্রিক রাজা অংশুদেব সন্ধের সময় মহাকালদেবীর বেদীতে এক অল্প বম্বেসী মা আর তার। দশ মাসের শিশুকে একসাথে উৎসর্গ করল। রাতে দেবী স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, পরদিন আবার যখন যুদ্ধ শুরু হবে, তখন বলি দেয়ার খড়গটি নিয়ে রাজাকে যেতে হবে যুদ্ধের ময়দানে। তবে দুপুর হওয়া পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে। দুপুরে যুদ্ধের ময়দানে নামাজ পড়তে দাঁড়াবেন তুরকান শাহ। এটা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য। এই সময় পশ্চিম আকাশের দিকে তাকিয়ে অংশুদেব যদি দেখে তিনটে শকুন চক্রাকারে ঘুরছে, তা হলে সাঁথে সাথে আঘাত হানবে সে।
পরদিন সকাল বেলা আবার যুদ্ধ শুরু হলো। রাজার। সৈন্য মরতে লাগল কাতারে কাতারে। দুপুর নাগাদ তুরকান শাহর বাহিনী রামপুরের প্রায় কাছাকাছি চলে এল। রাজধানীর পতন হবে যে-কোনও মুহূর্তে। ধৈর্য হারাল না রাজা। অক্ষরে অক্ষরে পালন করল দেবীর নির্দেশ। পশ্চিমাকাশে শকুন। চোখে পড়তেই খড়গ হাতে নিয়ে কালো কুচকুচে মাদী ঘোড়ায় চেপে তুরকান শাহ বাহিনীর কেন্দ্র লক্ষ্য করে ছুটে গেল অংশুদেব। দরবেশের যোদ্ধারা দেখল অন্ধকার ছায়ার মত কী একটা তাদের পাশ কাটিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে যাচ্ছে। তুরকান শাহ তখন রুকুতে। জয় মা মহাকালদেবী বলে খড়গের এক কোপে দরবেশের ধড় আর মাথা আলাদা করে ফেলল তান্ত্রিক রাজা। ঠিক সেই মুহূর্তে শোনা গেল। বজ্রপাতের প্রচণ্ড শব্দ, ঘনিয়ে এল আঁধার। তুরকান শাহর বাহিনী অবাক হয়ে দেখল, দরবেশের মাথা শূন্যে উড়তে উড়তে চলে গেল বহুদূরে। হারিয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে। মহাকালদেবীর জয় বলে ছুটে এল রাজার সৈন্যরা। নতুন মনোবল নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তুরকান শাহর বাহিনীর ওপর। কচুকাটা হয়ে গেল সব দরবেশ আর নতুন যারা মুসলমান হয়েছে।
যুদ্ধ শেষ হলে রাজার ভাই খেজুরচণ্ড মহাকালদেবীর তান্ত্রিক পুরোহিতদের নিয়ে তুরকান শাহর লাশ উঠিয়ে আনার চেষ্টা করেছিল। উদ্দেশ্য, দেবীর বেদীতে লাশ উৎসর্গ করা। তবে সে আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি। হাতি দিয়ে টেনেও লাশ ওঠাতে পারেনি তান্ত্রিকেরা। বাধ্য হয়ে গভীর এক গর্ত খুঁড়ে লাশ পুঁতে ফেলে তারা। ওখানেই এখন তুরকান শাহ শহীদের মাজার। এরপর কেটে গেল বহুদিন। তান্ত্রিক রাজা অংশুদেব আর খেজুরচণ্ড ততদিনে কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। রাতদিন চলছে মহাকালদেবীর পুজো আর নরবলি। ঠিক সেই সময়ে দেখা দিল আরেক দরবেশ। এঁর নাম শাহ মখদুম রূপস। ইনি সাদা কাপড়ে সব সময় মুখ ঢেকে রাখতেন। তার আসল চেহারা কেউ কখনও দেখেনি। স্বয়ং বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ) এঁর পরদাদা। তুরকান শাহ হত্যার প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর শাহ মখদুম। অংশুদেব আর খেজুরচণ্ডের সাথে তার সংঘর্ষ হয়ে উঠল অনিবার্য। তবে রূপস তুরকান শাহের মত ভুল করলেন না। তিনি জানতেন, মহাকালদেবীর পুজো করে করে দেবীর কৃপায় অংশুদেব এক অনন্য শক্তির অধিকারী। এর মুখোমুখি হতে হলে তান্ত্রিকদের বিষয়ে ব্যাপক জ্ঞান আছে এমন ব্যক্তির পরামর্শ দরকার। ভাগ্য ভাল ছিল দরবেশের। বাংলায় তখন ইসলাম প্রচার করছেন শাহ সুলতান মাহিসওয়ার। তান্ত্রিকের যম এই সুফি দরবেশ। ইনি এদেশে এসেছিলেন পানিপথে। মাছের আকারের এক নৌকোয় করে। লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল দরবেশ মাছের পিঠে চড়ে এসেছেন। তার নাম হয়ে গেল মাহিসওয়ার। চিটাগাং-এ পা রেখেই তিনি জানতে পারেন নোয়াখালির দক্ষিণে সমুদ্রপাড়ে হরিরামনগর বলে এক সমৃদ্ধ নগরী আছে। এখানকার রাজা বলরাম অতি বড় তান্ত্রিক এবং ভয়ানক অত্যাচারী। দরবেশ বুঝলেন, জনগণের মন জয় করতে হলে এই অজেয় রাজাকে যুদ্ধে হারিয়ে আমজনতার সামনে এর শিরচ্ছেদ করতে হবে।
তান্ত্রিকদের শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস হলো তারা যে দেবী মূর্তির পুজো করে, সেই দেবী মূর্তি। যুগের পর যুগ অসংখ্য নরবলি মন্ত্র সাধনা এবং হোম আর পুজোর পরই কেবল ধীরে ধীরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় এসব মূর্তিতে। এরা হয়ে ওঠে জাগ্রত। এসব মূর্তির সামনে রেখে মন্ত্রপূত করা হয় ত্রিশূল কিংবা খড়গ। প্রায় অজেয় হয়ে ওঠে ওই সব বিশেষ অস্ত্রের মালিকেরা। দরবেশরা প্রচুর অর্থের বিনিময়ে কোনও দুর্বল চরিত্রের অর্থলোভী তান্ত্রিক পুরোহিতকে দলে ভেড়াতেন। বলরামের বেলায় বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তার এক মন্ত্রীও। আউলিয়ারা কোরবানি করা বকনা গরুর রক্ত তামার পাত্রে ধরে রাখতেন। দরবেশদের কথামত গোরক্ত দিয়ে দেবীর চরণ ভেজাত দলছুট পুরোহিত। এরপর তারা ওই রক্ত ছিটিয়ে দিত মন্দিরের চারপাশে। মন্ত্রপূত ত্রিশূল বা খড়গ রাখা হত দেবীর পায়ের কাছে। গোরক্ত মাখিয়ে দেয়া হত ওগুলোতেও। এ কাজগুলো সমাধা হওয়ার পরপরই চালানো হত আক্রমণ। তান্ত্রিক রাজারা যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে হতভম্ব হয়ে দেখত, দেবীর কোনও শক্তিই কাজ করছে না আর। মুসলমান যোদ্ধাদের কাছে সম্পূর্ণ অসহায় তারা। যুদ্ধে পরাজিত রাজা আর তার সেনাপতিদের শিরচ্ছেদ করা হত। মন্দিরের সামনেই। তান্ত্রিকতার বিনাশ সুফিবাদের সূচনা।
শাহ মখদুম রূপস মাহিসওয়ারের পরামর্শে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে অংশুদেবের প্রধান পুরোহিতের শ্যালক পঞ্চানন পাণ্ডেকে হাত করলেন। অবশ্য এর পেছনে অন্য ঘটনাও আছে। চল্লিশজন স্ত্রীর গর্ভে অংশুদেবের পঞ্চাশটা ছেলেমেয়ে জন্মেছিল। এদেরই মধ্যে এক মেয়ে ছিল অনন্য সুন্দরী। মেয়েটিকে দেখে হুঁশজ্ঞান হারিয়ে ফেলে পঞ্চানন। প্রেম নিবেদন করে বসে। সাধারণের জন্যে রাজার মেয়েকে বিয়ে করা কিংবা তার সাথে প্রেম করার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। প্রধান পুরোহিতের মুখের দিকে তাকিয়ে অংশুদেব পঞ্চাননকে শূলে চড়াল না বটে, তবে তার নাক-কান কেটে দিল। প্রতিহিংসায় দ্বিতীয়বার হুশ হারাল পঞ্চানন। অংশুদেবকে ঝাড়েবংশে শেষ না করে তার শান্তি নেই। তারপর যা হওয়ার তাই হলো। শাহ মখদুম রূপসের সাথে যুদ্ধে হেরে গর্দান হারাল অংশুদেব আর তার ভাই খেজুরচণ্ড। রাজার মেয়েটিকে পেতে ছেয়েছিল পঞ্চানন। তবে শাহ মখদুম রূপস তাতে রাজি হননি। ঘটনা জানাজানি হয়ে যেতে পারে এই ভয়ে টাকা-পয়সা নিয়ে সে পালিয়ে গিয়েছিল বহুদূরের কোশল রাজ্যে। আত্মগোপন করে থাকা রাজার অনুসারী কিছু তান্ত্রিক বিষয়টি আঁচ করতে পেরে একরাতে প্রধান পুরোহিতের বাড়ি আক্রমণ করে ওটাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। বহুদিন ওই ভিটে ছিল পরিত্যক্ত। এর অনেকদিন পর ওখানে আবার বাড়ি তৈরি করে ওই পুরোহিতের বংশধরেরা। ওই পুরোহিতেরই নাতির নাতি তস্য নাতি হলো তোদের এই সিধু জ্যাঠা, বুঝলি কিছু রে, বেন্দাবন?
সিধু জ্যাঠা নানান ধরনের তত্ত্বকথাও শোনাতেন। একদিন বললেন, বুঝলি, বেন্দাবন, এই জগৎ সংসার হলো ভাল আর মন্দের যুদ্ধক্ষেত্র, শুম্ভ নিশুম্ভের লড়াই। কে ভাল কে মন্দ সেটি নিয়ন্ত্রণ করে নিয়তি। তোর কথাই ধর। যদি ওই বৌদ্ধ মন্দিরে যেতিস, তুই হতি লোকনাথ বাবার মতন বিরাট সাধু। সেখানে না গিয়ে তুই গেলি চিত্রকূটের গুহায়। বদলে গেল তোর নিয়তি, তোর পথ হলো পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিকের। আমার কথা শোন, এই লাইনে এসেই যখন পড়েছিস, তখন ভাল করে তন্ত্রমন্ত্র শেখ। তবে এজন্যে তোকে সবচেয়ে আগে শিখতে হবে পালি। এ হচ্ছে গৌতম বুদ্ধের ভাষা। থিরুরা দাবি করে দুনিয়ায় পালির মত নিখুঁত কোনও ভাষা নেই। পৃথিবীর সবকিছু বদলে যেতে পারে, শুধু পরিবর্তন হয় না পালির। দেবতা, অপদেবতা, আল্লাহ, ভগবান, ঈশ্বর কেউই মূখের প্রার্থনা পছন্দ করে না। প্রার্থনা হতে হবে সুমধুর, প্রাঞ্জল, হৃদয়গ্রাহী-যার ভাষা হবে নিখুঁত। জানিস তো ইউরোপ আমেরিকায় শয়তানের পুজো করতে ল্যাটিন ভাষা ব্যবহার হয়। আয়, আজ থেকে তোকে পালি শেখাই।
আট
সেই আমার পালি ভাষায় হাতে খড়ি। খুব ধীরে বছরের পর বছর ধরে পালি শিখলাম। তান্ত্রিকদের লেখা পুঁথিও পড়লাম বিস্তর। আদ্যিকালের পুঁথি পাণ্ডুলিপিতে সিধু জ্যাঠার ঘর ভর্তি। এ ছাড়াও অদ্ভুত সব পুরনো জিনিস ছিল তার সংগ্রহে। আপনি আমার বাসায় যে জিনিসগুলো দেখেছিলেন, সেসবই এই সিধু জ্যাঠার কাছ থেকে পাওয়া। অকৃতদার পুরুষ, ছেলেমেয়ে বা তিনকুলে কেউ নেই। আমাকেই সব দিয়ে গেছেন। ভীষণ অভিশপ্ত জিনিস ওগুলো। পিশাচ সাধনায় উপাচার হিসেবে এসব সামগ্রীর গুরুত্ব সীমাহীন।
সিধু জ্যাঠার মৃত্যু হয় ১৯৭১-এ স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়। ওই সময় হিন্দুপ্রধান রামপুর বোয়ালিয়া খান সেনাদের অন্যতম প্রধান টার্গেট হয়ে দাঁড়ায়। রাতদিন রাজাকার ইনফর্মার আর মিলিটারির আনাগোনা। জ্যাঠার তিরিক্ষি মেজাজের কারণে অনেকেরই রাগ ছিল তার ওপর। যে কোনও দিন হামলা হওয়ার সম্ভাবনা। সাবধানের মার নেই ভেবে একদিন খুব ভোরে বিরাট এক, ট্রাঙ্ক মাথায় করে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হলেন সিধু জ্যাঠা। বোনকে রেখে এসেছেন মামাদের বাড়িতে। বিড়ালদাহর কাছেই দাশুড়িয়া বর্ডার দিয়ে ভারতে পালিয়ে যেতে চান। ভারতে যাওয়ার বিষয়টি তখন তত সহজ ছিল না। যাব বললেই যাওয়া যায় না। রাজাকার মিলিটারিদের চোখে ধুলো দিলেও সর্বস্ব কেড়ে নেয়ার জন্যে পথে-প্রান্তরে ওঁৎ পেতে আছে অজস্র দালাল-চোর-ডাকাত। শরণার্থী পরিবারের সোনাদানা, টাকা-পয়সা সব কেড়ে নিয়ে মা-মেয়েকে সবার সামনে বলাৎকার করার ঘটনা তখন আকছার ঘটছে। যুবতী সুন্দরী মেয়ে দেখলে এরা অনেক সময় তাদের নিজেদের ফুর্তির জন্যে কাছেও রেখে দিত। তাকে বললাম, দাদু, আপনাকে কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। এলাকার বিশ্বস্ত কোনও দালালের সাথে দিতে চাই আপনাকে আমি।
তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু কতদিন অপেক্ষা করতে, হবে আমাকে?
একেবারে দিনক্ষণ উল্লেখ করে তো কিছু বলতে পারছি না, দাদু। একদিনও হতে পারে আবার সাতদিনও হতে পারে। রাস্তা-ঘাটের অবস্থা, বর্ডারের পরিস্থিতি সব বুঝে তবেই না ব্যবস্থা।
এসব শুনে খুব একটা খুশি হতে পারলেন না জ্যাঠা। চুপ করে থাকলেন। বললেন, দেখ যা ভাল হয়…
আমাদের পাড়ার কদম রসুল সেই সময় লোক পারাপার করত। জনপ্রতি দুটো টাকা তার রেট। তবে লোক বিশ্বস্ত, সেই ছোটবেলা থেকে আমাদের বাড়িতে এর বাবার আসা যাওয়া। সিধু জ্যাঠা আমার গুরু। তাঁর কাছ থেকে সে কোনও টাকা চায় না। শুধু পথ-খরচা দিলেই হবে। জ্যাঠা ছাড়াও আরও চারজনকে নিয়ে এক বর্ষার রাতে রওনা হলো কদম রসুল। জ্যাঠা তাঁর পাঁচমণি তোরঙ্গ মাথায় করে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কদম রসুল হেসে বলল, স্রেফ টাকা-পয়সা ছাড়া আর কিছুই সাথে রাখা যাবে না, বাবু। ওই গন্ধমাদন মাথায় করে যেতে দেখলে আমার আপন ভাইও আপনার গলা ফাঁসিয়ে দেবে। কী আর করা, তোরঙ্গ আমার জিম্মায়। রাখতে হলো তাকে।
বর্ডারে পৌঁছতে হলে পনেরো মাইলটাক হাঁটতে হবে। তবে রাস্তা সহজ নয়। বাঁশঝাড়, খেতের আল, আমবাগান, দিঘির পাড়, বাড়ির আঙিনা এসবের ভেতর দিয়ে যাত্রা। অন্ধকারে নিতান্ত প্রয়োজন না হলে টর্চের আলো ফেলা যাবে না। ডাকাত আর লুটেরার দল হায়েনার মত ওঁৎ পেতে আছে সবখানে। সারারাত হেঁটে ছোট্ট দলটি নদীর কাছে যখন পৌঁছল, তখন ভোর হতে আর বেশি বাকি নেই। পাড়ের কাছেই লগিতে নৌকো বেঁধে অপেক্ষা করছে কদম রসুলের কন্ট্যাক্ট। একদল রাজাকার রাতের রোদ শেষে ক্যাম্পে ফিরছিল সেই সময়, ভিতুর ডিম রাজাকাররা জ্যাঠাদের দলটাকে মুক্তিযোদ্ধা মনে করে খান সেনাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে দুতিন রাউণ্ড ফায়ার করে বসল। ভয় পেয়ে জ্যাঠার দলের লোকেরা হুড়মুড় করে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেউ একজন জ্যাঠাকেও ধাক্কা দিয়ে থাকবে।
ভাল সাঁতার জানতেন সিধু জ্যাঠা। নৌকোয় নিজে তো উঠলেনই, সেই সাথে চুলের মুঠি ধরে আরও দুজনকে উঠিয়ে নিলেন। বাজখাই গলায় মাঝিকে বললেন নাও ছাড়তে। জ্যাঠারা যখন মাঝ গাঙে তখন পাড়ে এসে উপস্থিত হলো মিলিটারি। দুদিন আগে মুক্তিযোদ্ধাদের এক অপারেশনে চারজন জওয়ান হারিয়েছে তারা। আবারও আক্রমণ হতে পারে ভেবে প্রস্তুতি নিয়েই রেখেছিল। বর্ষার পদ্মা ভয়ঙ্করী, যেমন খরস্রোতা তেমনই চওড়া। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে খান সেনারা জানত, মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ শেষে নৌকো করে খুব দ্রুত রেঞ্জের আড়ালে চলে যায়। এবার মিলিটারি ন্যূনতম একমাইল রেঞ্জের হেভি মেশিনগান সাথে নিয়ে নদীর পাড়ে এসেছে। নৌকোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে জ্যাঠা। ছেষট্টি ক্যালিবারের হেভি মেটাল বুলেট ছিন্নভিন্ন করে ফেলে তার দেহ। এসবই পরে কদম রসুলের কাছ থেকে শোনা।
নয়
এখন মূল ঘটনায় আসি। আগেই বলেছি নানা কথা বলতেন সিধু জ্যাঠা আমাকে। শীলাদেবীর কথাও উনিই প্রথম আমাকে শোনান। শাহ সুলতান মাহিসওয়ার পুরাজ্যের রাজধানী মহাস্থান গড় দখলের জন্যে বদ্ধপরিকর। তখন এখানকার রাজা ছিল পরশুরাম। তবে আসল ক্ষমতা ছিল পরশুরামের বোন শীলাদেবীর হাতে। শীলাদেবী ছিল সে যুগের সব থেকে বড় তান্ত্রিক। অনিন্দ্যসুন্দরী এই যুবতী পুজো করত জরাসুরের। ভয়ানক নিষ্ঠুর এই যক্ষের চরণে সে নিবেদন করেছিল নিজেকেই। মহাস্থান গড়ের জীয়তকুণ্ড শীলাদেবীকে এই যক্ষই দান করে। এই শীলাদেবী প্রায়ই ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা দেখতে পেত। শীলাদেবী বুঝতে পেরেছিল, মাহিসওয়ার জীয়তকুণ্ড ধ্বংস করবেন এবং পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। এর থেকে মুক্তির উপায় বের করার জন্যে সে এক পরিকল্পনা করে। তার খুব বিশ্বস্ত চারজন অনুচরকে প্রাচীন আর্যদের মূলধারার যে তান্ত্রিকতা সেটির খোঁজে পাঠায়। এই চারজনের ভেতর একজন ছিল অংশুদেবের প্রধান পুরোহিতের বড় ছেলে বজ্ৰযোগী। সিধু জ্যাঠার মতে বজ্রযোগীর মত বড় তান্ত্রিক বঙ্গদেশে অতি বিরল। সিধু জ্যাঠা আমাকে এর বেশি আর কিছু বলেননি।
১৯৭৩ সালের দিকে আমাদের এখানে নকশাল আন্দোলন চরমে ওঠে। মোটামুটি অবস্থাসম্পন্ন লোকদের ধরে সর্বহারারা পটাপট মেরে ফেলতে লাগল। এদের কেউ কেউ নানা উপদলে ভাগ হয়ে লুটতরাজ করতেও লেগে গেল। জ্যাঠার ফেলে যাওয়া তোরঙ্গে মূল্যবান কিছু আছে কি দেখার জন্যে একদিন সকালে খুললাম ওটা। তোরঙ্গের ভেতর অনেক কিছুর সাথে ভেড়ার নরম সাদা চামড়ায় শুদ্ধ পালিতে লেখা এই স্কুলটি পেয়েছিলাম। বরেন্দ্র অঞ্চলে মধ্যযুগে পালি ভাষায় যত কিছু লেখা হয়েছে, তার ভেতর একটি অনন্য সাধারণ লেখা এটি। আপনাকে দেখানোর জন্যেই সাথে করে নিয়ে এসেছি আমি। স্ক্রলটি হাতে দিতে যাবে এমন সময় বাবুর্চি এসে খবর দিল খাবার রেডি। বাইরে তাকিয়ে দেখি বৃষ্টি ধরে এসেছে, সেই সাথে কারেন্টও চলে এল। স্ক্রল রয়ে গেল বৃন্দাবন ঘটকের হাতেই। খাওয়া-দাওয়া সেরে পাশাপাশি দুটো বিছানায় শুয়ে পড়লাম আমরা দুজন।
ঘুম ভেঙে দেখলাম সকাল নটা বাজে। পাশের বিছানা খালি, বিদায় হয়েছেন বৃন্দাবন ঘটক। সকালে উঠেই খালি পেটে পানি খাওয়া আমার অনেক দিনের অভ্যেস। বেড সাইড টেবিলে পিরিচে ঢাকা কাঁচের গ্লাসে পানি থাকে। পানির গ্লাস হাতে নিতে যেয়ে দেখি সেই স্ক্রলটি ওখানে। রাখা। পানি খেয়ে বাথরুম সেরে স্ক্রলটা হাতে নিয়ে বসলাম। কালো কালিতে পাখির পালক দিয়ে চিকন হরফে শুদ্ধ পালিতে যে কথাগুলো লেখা, সেটি সরল বাংলায় অনুবাদ করলে এই রকম দাঁড়াবে:
১২২৩ শতাব্দে তিব্বতের নিকট তান্ত্রিক মহাপুরুষ শ্রীমান চিত্রকূট মহাশয়ের সাধন পীঠে বসিয়া আমি বজ্ৰযোগী এই পুঁথি রচনা করিতেছি। ১২২১ শতাব্দে শীলাদেবী পুণ্ড্রনগরী হইতে একদল অনুচরকে তন্ত্রসাধনার বিষয়ে সম্যক অবগত হইবার অভিপ্রায়ে দিকে-দিকে প্রেরণ করেন। ক্রমে এক বৎসরকাল অতিক্রম হইল, অথচ কেহই ফিরিয়া আসিল না। অতঃপর দেবী তাহার একান্ত বিশ্বস্ত দশজন অধ্যক্ষ পুরোহিতের মধ্য হইতে চারজনকে পুনরায় এতদঅভিপ্রায়ে ভারতবর্ষের চতুর্দিকে প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন। আমাদিগের চারজনকে ঋক, সাম, যজুঃ, অথর্ব এই চারটি সাঙ্কেতিক নামে ভূষিত করা হইল। আমি সর্বকনিষ্ঠ বিধায় আমার নাম হইল অথর্ব। আমাদিগকে চার বৎসরকাল স্বাচ্ছন্দ্যে কাটাইবার নিমিত্তে প্রচুর অর্থ প্রদান করা হইল।
একদিন অতি প্রত্যূষে আমরা চারজন পুণ্ড্রনগরী হইতে যাত্রা করিয়া বুড়িগঙ্গা নদীর তীরবর্তী ঢাকা-ঈশ্বরী মন্দিরে পৌঁছাইলাম। এই স্থলে মাটির গভীরে দশভুজা দেবী সহস্রাদি গুপ্তাবস্থায় ছিলেন। আরাকানের বিতাড়িত মঙ্গত রায় ওরফে রাজা বল্লাল সেন এস্থলে যাত্রাবিরতিকালে দেবী তাহাকে স্বপ্নে দর্শন দেন। বল্লাল সেন আপাদমস্তক স্বর্ণনির্মিত দশভুজাকে উত্থিত করিয়া দেবীর সম্মানে মন্দিরটির নির্মাণ করেন। দশভুজা ঈশ্বরী নামেও পরিচিত লাভ করিয়াছেন। ঈশ্বরী বহুকাল ভূমিতলে গুপ্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ঢাকা-ঈশ্বরী বলা হয়। কিন্তু আমরা দশভুজা দর্শনে এস্থলে আগমন করি নাই। আমরা আসিয়াছি চতুর্ভুজ দেবতা বাসুদেব দর্শনে। বাসুদেব আরাকানী বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের প্রধান উপাস্য দেবতা। যাত্রার পূর্বে তাহার কৃপা লাভ করাই আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য, ইহাই শীলাদেবীর নির্দেশ। পরদিন প্রত্যূষে আহার সমাপনান্তে ঋক আরাকান রাজ্যে গমনের অভিলাষে বুড়িগঙ্গা নদীপথে শাগঙ্গার (বর্তমানে চট্টগ্রাম) উদ্দেশে যাত্রা করিল। সাম কামরূপ রাজ্যে গমনের অভিপ্রায়ে পূর্বদিকে সড়কপথে যাত্রা করিল। আমি এবং যজুঃ আরও একদিবস ঢাকেশ্বরী মন্দিরে অতিবাহিত করিলাম এবং অপরাহ্বে নদীতীরে ভ্রমণ করিতে বাহির হইলাম। আমরা লক্ষ করিলাম সেই স্থলে একশ্রেণীর তন্তুবায়ের বাস। তাহারা অতি সূক্ষ্ম তন্তু দ্বারা এক বিশেষ শ্রেণীর বস্ত্র উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। এই বস্ত্র মসলিন নামে খ্যাত। বোয়াল নামক এক জাতীয় আঁশহীন বৃহৎ মৎস্যের সূক্ষ্ম দাঁতের সারি ব্যবহার করতঃ উক্ত মসলিন বস্ত্রের তন্তু সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ও মসৃণ করা হয়। এই বস্ত্রশিল্পে নারীদের অবদানই অধিক। মসলিন মহামূল্য বস্ত্র হইলেও ইহার প্রস্তুতকারীরা অত্যন্ত দীনহীন। সুষম খাদ্য ও পুষ্টির অভাবে তাহাদের দেহকাণ্ড ক্ষীণ ও নজ। পরিধেয় বস্ত্র অতি মলিন ও শতচ্ছিন্ন। আমি আরও এক শ্রেণীর কুশলী দেখিতে পাইলাম। উহারা শঙ্খ দ্বারা নানা প্রকার দ্রব্য সামগ্রী এবং অলঙ্কার প্রস্তুত করিতেছে। এই কর্মেও নারীদের অবদানই অধিক। সূর্যাস্তকালীন সময়ে আমরা নগরী পরিভ্রমণ শেষে মন্দিরে ফিরিয়া আসিলাম। মন্দিরে অনেক সেবাদাসী রহিয়াছেন। ইহাদের অধিকাংশই অযোধ্যা ও মহারাষ্ট্র হইতে আগত। এইসব রমণীদের দেহ, সৌন্দর্য যে কাহারও মনোবিকার ঘটাইবে। আগামীকাল প্রত্যূষে এস্থল ত্যাগ করিতে হইবে।
পরদিন যথা সময়ে পশ্চিম দিকে যাত্রা করিলাম এবং দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া সূতানাটি গোবিন্দপুর (বর্তমানে কোলকাতা) নামক এক প্রখ্যাত নগরীতে পৌঁছাইলাম। এই নগরী গঙ্গা নদীতীরে অবস্থিত। এই অঞ্চলে ছোট ছোট কুটিরে কলি বাজলজ শামুক হইতে প্রচুর পরিমাণে চুন এবং নারিকেল হইতে কাতা বা রজু উৎপন্ন করা হয়। নগরীতে প্রচুর সংখ্যক পান্থশালা রহিয়াছে। আমরা উহার একটিতে আশ্রয় লইলাম। এই নগরীর অধিবাসীগণ দেবী স্বরস্বতীর বর লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা প্রায় সকলেই শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং শিক্ষাক্ষেত্রে খুবই অগ্রগণ্য। পরদিন অপরাহে যজুঃ আমার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্বক কলিঙ্গ রাজ্যে গমনের লক্ষ্যে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিল। এই ক্ষণে আমি সম্পূর্ণ একাকী বোধ করিলাম। সহচরেরা সকলেই বিদায় লইয়াছে। আমি কোন স্থানে কাহার নিকট যাইব সে সম্পর্কে কিয়ৎ পরিমাণ জ্ঞান নাই। তৎক্ষণে অন্যমনস্ক হইয়া গঙ্গা নদীর তীর দিয়া হটিতে লাগিলাম। গঙ্গার তীর অতীব মনোমুগ্ধকর। এ স্থলে কালক্ষেপণ করিলে হৃদয় ভাবাবেগে পূর্ণ হয়। ক্রমান্বয়ে আমি নগরী হইতে দূরে সরিয়া গেলাম। অরুণাচল অস্তগামী হইল। আমি কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামের লক্ষ্যে একটি আশ্রয়স্থল সন্ধান করিতে লাগিলাম। অদূরে একটি বৌদ্ধ মঠ দৃষ্টিগোচর হইল। গঙ্গার তীর ঘেঁষিয়া উহার অবস্থান। লাল ইষ্টক নির্মিত এই মঠটির স্থাপত্যশৈলী অতি মনোরম। ইহার মেঝে কালো কষ্টি পাথরে নির্মিত। একটি আয়তক্ষেত্রের আকৃতি বিশিষ্ট এই মঠটির সম্মুখভাগে একটি কূপ রহিয়াছে। কূপের পাশে কাষ্ঠ নির্মিত একটি পাত্রের সহিত লম্বা রঞ্জু সংযুক্তাবস্থায় দৃষ্টিগোচর হইল। ওই কাষ্ঠ নির্মিত আধারটি কূপে নিক্ষেপ করতঃ জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া সেই জল উপরে উত্তোলন কারলাম। জল পান করিয়া আমার প্রাণ জুড়াইয়া গেল। মঠটির চতুর্দিকে কৃষ্ণচূড়া ও কদম্ব বৃক্ষের সারি। আমি মঠটির অভ্যন্তরে পূজা মণ্ডপের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। অথচ বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারিলাম কিয়ৎক্ষণ পূর্বেই অকুস্থলে পূজাপাঠ ইত্যাদি সমাপন হইয়াছে।
মঠের একটি স্তম্ভে হেলান দিয়া হস্তপদ ছড়াইয়া অর্ধশায়িতাবস্থায় আমি বৃক্ষসারির মধ্য দিয়া গঙ্গার প্রবাহিত স্রোতধারার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। অস্তগামী সূর্যদেবের লাল কিরণমালায় সে স্রোতধারার নৈসর্গিক সৌন্দর্য অতুলনীয়। ক্রমে আমার চেতনা লুপ্ত হইল। আমি গভীর নিদ্রায় আপতিত হইলাম। এবং নিদ্রাকালীন সময়ে অভূতপূর্ব এক স্বপ্ন দর্শন করিলাম। দেখিতে পাইলাম, মঠের প্রধান পুরোহিত এক পকূকেশ বৃদ্ধ আমাকে প্রশ্ন করিলেন কী উদ্দেশে আমি এ স্থলে আগমন করিয়াছি। উত্তর করিলাম, প্রভু, রাজ আজ্ঞা হেতু আমাকে অকুস্থলে আসিতে হইয়াছে। সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ কিয়ৎক্ষণ আমার দিকে চাহিয়া উত্তর করিলেন, শীলাদেবী ও তদীয় ভ্রাতা পরশুরামের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিয়াছে। তাহাদের আর কোনও আশা নাই। তাঁহাদের রাজ্য হারাইতে হইবে। তুমি এই ক্ষণে শীলাদেবীর নিকট প্রত্যাবর্তন কর। আমি উত্তর করিলাম, হে, প্রভু, যে উদ্দেশ্যে দেবী আমাকে প্রভূত অর্থ প্রদান করতঃ প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা আমাকে সফল করিতে দিন। পকূকেশ সেই বৃদ্ধ আমাকে সুগভীর দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিয়া ক্ষণকাল পর উত্তর করিলেন:
হে, বৎস, তোমাকে সুদীর্ঘ পথ পরিক্রম করিতে হইবে। তিব্বতের দুর্গম লাসা নগরীর নিকটে এক পর্বত গুহায় জনৈক সিদ্ধ পুরুষ বাস করেন তাহার নাম চিত্রকুট। স্বীয় সাধনা বলে ওই পুরুষ মোক্ষ লাভ করিয়াছেন। তিনি আঁধার জগতের মহাপ্রভুর সাধনা করেন। তাঁহার সাধন পীঠ এস্থল হইতে ছয় মাসের পথ। লাসা নগরীর নিকটবর্তী হইলে হিমালয়ের বরফ মুণ্ডিত দুইটি চূড়া তোমার দৃষ্টিগোচর হইবে। উক্ত স্থানে একটি বৌদ্ধ মন্দির দেখিতে পাইবে। ইহার অদূরে পর্বত গাত্রে একটি সুড়ঙ্গের ন্যায় গুহা আছে। সূর্যাস্তকালীন সময়ে সেই গুহা হইতে ধূম্র নির্গত হইতে দেখিবে। উহাই চিত্রকূটের সাধন পীঠ। স্মরণ রাখিও, চিত্রকূট কাপালিক নহেন। সুউচ্চ স্তরের তন্ত্র সাধনাই তাহার ব্রত। এই সাধনায় স্বীয় সত্তাকেই অন্ধকার রাজ্যের মহাপ্রভুর নিকট উৎসর্গ করিতে হয়।
আমার নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলাম রাত্রির অমানিশা কাটিয়াছে। চতুর্দিকে পক্ষীকুল কুজন করিতেছে। তৎক্ষণাৎ সে স্থল পরিত্যাগপূর্বক আমি পান্থশালায় প্রত্যাবর্তন করিলাম ও আমার ভ্রমণের সরঞ্জামাদি লইয়া তিব্বতাভিমুখে যাত্রা করিলাম। দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইল। অবশেষে আমি এক পার্বত্য জাতি অধ্যুষিত নগরীতে প্রবেশ করিলাম। সুউচ্চ ভূমিতে অবস্থিত সেই নগরীর নাম থিষ্ণু। এই জাতির মধ্যে ব্যভিচার ও অনাচার অতি মাত্রায় অনুপ্রবেশ করিয়াছে। অসম বিবাহ, অতি মাত্রায় সোমরস পান, কুরুচিপূর্ণ অশ্লীল নর্তন কুর্দন ইহাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটাইয়াছে এবং মানবিক গুণাবলীর ধ্বংস সাধন করিয়াছে। এ স্থলে আসিয়া আমি রাত্রি যাপনের নিমিত্তে একটি পান্থশালায় আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। সন্ধ্যা পরবর্তী সময়ে সংক্ষিপ্ত বস্ত্রে আচ্ছাদিত বারবণিতারা আমাকে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিল। ইহাদের মধ্যে আমি একটি বালিকাকে দেখিতে পাইলাম। উক্ত বালিকা সকলের পশ্চাতে দণ্ডায়মান ছিল। দীনহীন বালিকাটিকে দেখিয়া আমার হৃদয় আর্দ্র হইল। চল্লিশোর্ধ্ব জনৈক বারবণিতাকে কিঞ্চিত অর্থ প্রদান করিয়া তাহার সহযোগিতায় উক্ত বালিকাটিকে আমার কক্ষে প্রবেশ করাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিলাম।
বালিকাটি ভীতা হরিণ শাবকের ন্যায় আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। আমি লক্ষ করিলাম, তাহার দেহ প্রকম্পিত হইতেছে। বালিকাটিকে আমার শয্যার উপর উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলাম। অতঃপর উহাকে অভয় দান পূর্বক তাহার পরিচয় ইত্যাদি জ্ঞাপন করিতে বলিলাম। বালিকাটির পিতা দীর্ঘদিন হইল নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তাহার মাতা নগরীর শাসকদের মনোরঞ্জন করিত। বর্তমানে তাহার স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়াছে এবং সে জটিল রোগে অতিশয় পীড়িতা। বালিকাটি অনন্যোপায় হইয়া অর্থোপার্জনের লক্ষ্যে বারবণিতাদের সহিত যুক্ত হইয়াছে। ইতিপূর্বে বিকৃতরুচিপূর্ণ একজন প্রৌঢ় তাহাকে এক পান্থশালায় বিগত রজনী হইতে অদ্য দ্বিপ্রহর অবধি নির্যাতন করিয়াছে। বালিকাটির বাহু, কপোল এবং গলদেশে অত্যাচারের চিহ্ন বিদ্যমান। দ্বিপ্রহরে প্রৌঢ় ব্যক্তিটি আহার সংগ্রহে বাহির হইলে বালিকাটি উক্ত পান্থশালা হইতে সবেগে প্রস্থান করিয়াছে। সে ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত। তাহার মাতা ও ছোট একটি ভ্রাতা পথ চাহিয়া আছে। শূন্য হাতে সে ফিরিবে কী প্রকারে?
অতঃপর আমি বালিকা সমভিব্যাহারে উহার মাতার পর্ণ কুটিরে উপস্থিত হইলাম ও বালিকার বাটীতে সপ্ত দিবস অতিবাহিত করিয়া তাহার মাতার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলাম। ইত্যবসরে বালিকার মাধ্যমে ঔষধপত্র, আহার ও বস্ত্রের ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়াছি। কুটির হইতে আমি কদাপি বাহির হইয়াছি। তাহার কারণ এই নগরীর নাগরিকেরা আদর্শহীন কপট শ্রেণীর। আমাকে অসহায় ভিনদেশী মনে করিয়া সর্বস্ব হরণ করিতে পারে। বালিকার মাতার সহিত আমার আলাপচারিতা হইয়াছে। উক্ত রমণীর পিতার আবাস লাসা নগরীর সন্নিকটে। তিব্বত গমনের অতি সহজ পথ নির্দেশ তাহার নিকট হইতে লাভ করিয়াছি। ইহাদের একরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে বিধায় অষ্টম দিবসে অতি প্রত্যূষে বালিকাটির শিয়রে কিঞ্চিৎ অর্থ রাখিয়া তিব্বতের পথে নির্গত হইলাম। আমার নির্গমন সম্বন্ধে বাটীর কেহই কিছু জানিতে পারিল না। সুদীর্ঘ দুর্গম পথ পরিক্রম করিয়া অবশেষে আমি লাসা নগরীতে উপস্থিত হইলাম। লাসার নাগরিকদের নিকট প্রশ্ন করিয়া নির্দেশিত স্থানের কোনও হদিশ পাইলাম না। পঞ্চদশ দিবসে নগরীর চতুর্দিকে ক্রমাগত পরিভ্রমণ করিলাম। অথচ কোনও স্থলে ওই বিশেষ বৌদ্ধ মন্দির বা পর্বত শঙ্খ দৃষ্টিগোচর হইল না।
দেশ ত্যাগের পর ষান্মাসিক কাল অতিবাহিত হইতে চলিল। ঋক, সাম, যজুঃ-র কথা স্মৃতিপটে ভাসিয়া ওঠে, ঈশ্বর বলিতে পারেন তাহারা কে কোথায় অবস্থান করিতেছে। এক দিবসে প্রচুর শৈত্য প্রবাহ হইতে লাগিল। আমি পান্থশালার বিশাল চুল্লির অগ্নিকুণ্ডের নিকট বসিয়া আমার পরবর্তী কর্তব্য বিষয়ে চিন্তাক্লিষ্ট ছিলাম। এমতাবস্থায় এক বৃদ্ধ ভিক্ষুনী সে স্থলে প্রবেশ করিল। তাহার সমগ্র পরিচ্ছদ তুষারাবৃত। মুখ মণ্ডল ও হস্তপদ নীলবর্ণ ধারণ করিয়াছে। তাহার চক্ষুদ্বয় ক্লান্ত ও হতাশাপূর্ণ। আমি সেই বৃদ্ধা রমণীকে তাহার জগদ্দল আভরণ হইতে মুক্ত হইতে সহায়তা করিলাম। তাহাকে উষ্ণ বলকারক এক জাতীয় বিশেষ তরল খাদ্যবস্তু (সুপ) ভক্ষণ করাইলাম। বৃদ্ধার হস্তপদ আপন হস্তদ্বারা উত্তমরূপে মর্দন করিয়া দিলাম। খাদ্য গ্রহণের পরপরই ভিক্ষুনী নিদ্রামগ্ন হইল। ভিক্ষুনীর নিদ্রা ভঙ্গ হইলে আমরা একত্রে মধ্যাহ্নের আহার গ্রহণ করিলাম। ভিক্ষুনী আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় হইল। সে আমার অত্র দেশে আগমনের হেতু জানিতে চাহিল। আমি অকপটে বৃদ্ধাকে সমস্ত বিষয় অবগত করাইলাম। সব শ্রবণ করিয়া ভিক্ষুনী ক্ষণকাল নিশ্চুপ রহিল। ইহার পর আমাকে আগামী দিবস প্রত্যষে ভ্রমণের নিমিত্তে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করিয়া বাহিরে নির্গত হইল।
আমি তাহার নির্দেশানুযায়ী পর দিবস প্রভাতে ভ্রমণে প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পর ভিক্ষুনী আবির্ভূত হইল। আমি উহাকে অনুসরণ করিয়া নগরীর উত্তর প্রান্তে উপনীত হইলাম। সুগভীর এক গিরিখাতের উভয় পার্শ্বে অতিকায় স্তম্ভের সহিত রঞ্জু সংযোগ করিয়া সেতুর ন্যায় একটি সংযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে। তুষারাবৃত সেই রঞ্জু সেতু তীব্র বায়ু প্রবাহে শূন্যে দোদুল্যমান। ভিক্ষুনী অতি কষ্টে সেই রঞ্জু সেতু অতিক্রম করিল এবং আমাকেও অনুরূপ করিতে আজ্ঞা করিল। আমি ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া সেই রঞ্জু সেতু অতিক্রম করিলাম। অতঃপর ক্রমাগত ঊর্ধ্ব মুখে উঠিতে লাগিলাম পর্বত সংলগ্ন একটি অতি সরু সড়ক বাহিয়া। সুতীব্র বাত্যাপ্রবাহ আমাদিগকে শূন্যে উড্ডীন করতঃ অনন্ত গহ্বরে। নিক্ষেপ করিতে চাহিল। দ্বিপ্রহর অতিক্রম হইলে আমরা পর্বতের শীর্ষদেশে উপস্থিত হইলাম। ভিক্ষুনী অঙ্গুলী নির্দেশে দূরবর্তী একটি অঞ্চলে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। নির্দেশিত পথে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একটি অতি মনোহর বৌদ্ধ মন্দির দেখিতে পাইলাম। উক্ত মন্দিরের কিয়ৎ দূরে একটি কৃষ্ণকায় পর্বত এবং তাহার অদূরে একটি বরাফাচ্ছাদিত পর্বতচূড়া আমার দৃষ্টিগোচর হইল। আমি হৃদয়ে তীব্র শিহরণ অনুভব করিলাম। এইক্ষণে ভিক্ষুনী আমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আপনার পথে যাত্রা করিল। পর্বতের ঈষৎ বক্র পৃষ্ঠদেশ বাহিয়া আমি গুহার পাদদেশে উপস্থিত হইলাম।
আনুমানিক দুই ক্রোশ পথ চলিবার পর বৌদ্ধ মন্দিরটি যে পর্বতশীর্ষে অবস্থিত, তাহার পাদদেশে পৌঁছিলাম। পশ্চিমাকাশে দিবাবসানের লাল আলোক। বৌদ্ধ মন্দিরে ঢং ঢং শব্দে ঘণ্টা বাজিল। তীব্র বাত্যাপ্রবাহে চতুর্দিকে তুষারকণা ছুটিতেছে। ঠিক সেই পর্বে আমি পর্যবেক্ষণ করিলাম কৃষ্ণ প্রস্তর নির্মিত নিকটবর্তী এক পর্বতের গুহা হইতে অনর্গল ধারায় ধূম্র নির্গত হইতেছে। সেইসব ধূম্রপুঞ্জ বিজাতীয় বীভৎস প্রাণীর রূপ ধরিয়া ঊধ্বাকাশে বিলীন হইয়া যাইতেছে। আমি ধীরে ধীরে উক্ত গুহার দিকে অগ্রসর হইলাম। গুহার সম্মুখভাগ একটি বৃত্তাকার সুড়ঙ্গের ন্যায়। অভ্যন্তরভাগে আগুন জ্বলিতেছে। কিঞ্চিত অগ্রসর হইলাম। বর্তুলাকার একটি প্রকাণ্ড কক্ষের এক প্রান্তে একটি কৃষ্ণকায় সুপুরুষের মূর্তি। কক্ষের মধ্যখানে শুভ্র পট্টবস্ত্র পরিহিত এক বৃদ্ধ বসিয়া অতি গম্ভীর ও মধুর স্বরে মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছেন। আমি উপলব্ধি করিলাম, এই পুরুষোত্তমই চিত্রকূট তান্ত্রিক। আমি তাঁহাকে আভূমি নত হইয়া প্রণাম করিলাম। কহিলাম, মহারাজ, আপনি যদি অত্র অধমকে তন্ত্র সাধনা শিক্ষা না দেন, তাহা হইলে এইক্ষণে ইহার বিনাশ সাধন করুন। অতি দূর রাজ্য হইতে আসিয়াছি। রাজ আজ্ঞা: আমাকে এই সাধনা শিখিতে হইবে। আমার উপর করুণা বর্ষণ করুন, মহারাজ।
চিত্রকূট তান্ত্রিক আমাকে শির উত্তোলন করিতে বলিলেন। এই প্রথম আমি তাহাকে পূর্ণ দৃষ্টি মেলিয়া দর্শন। করিলাম। তাঁহার গাত্র সম্পূর্ণ কেশহীন। পট্টবস্ত্রখানিতে কোথাও কোনও সেলাই বা সচিকর্মের চিহ্ন নাই। উজ্জল গৌরবর্ণ শরীর, শরের ন্যায় আঁখিপটের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। প্রথম দর্শনেই মহারাজকে আমার অত্যন্ত আকর্ষণীয় মানব বলিয়া মনে হইল। তিনি আমাকে স্নানের নির্দেশ ও পট্টবস্ত্র প্রদান। করিলেন। স্নান সমাপন করিয়া আমি উহা পরিধান করিলাম। মহারাজ আমাকে প্রত্যহ অন্ততপক্ষে তিনবার স্নান করিবার। নির্দেশ দিলেন। এই নিমিত্ত আমাকে ছয়টি পট্টবস্ত্র দান করিলেন। প্রতিবার স্নানের সময় বস্ত্রাদি উত্তমরূপে ধৌত করিবার আদেশ করিলেন। বর্তুলাকার কক্ষটিই তাঁহার উপাসনা গৃহ। সর্বদাই কক্ষটিকে ধৌত করতঃ উত্তম রূপে শুষ্ক বস্ত্রখণ্ড সহযোগে মুছিতে হয়। ইহা ছাড়াও আতর ও গোলাপের নির্যাস ছিটাইতে হয়। চন্দন তৈলের প্রদীপ জ্বালিতে হয়। তাহার আরাধ্য দেবতার নাম আহুরা বা পট্রহ এর রাজকুমার। মহারাজ সূর্য উদয় ও সূর্যাস্তের সময় স্বহস্তে দেবমূর্তিটিকে আতর ও গোলাপের জল মিশ্রিত করিয়া উক্ত জল দ্বারা ধৌত করেন। মহারাজ প্রাচীন পারস্য, মিশরীয় ও ইয়াহুদ নামক এক গোত্রের ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছেন। আমি ওই সকল ভাষা অধ্যয়ন করিতে পারি না। বলিয়া তিনি কিছু কিছু মন্ত্র সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।
মহারাজ সূর্য অস্ত যাওয়ার পর হইতে সূর্য উদয় পর্যন্ত উপাসনা করেন। মধ্যাহ্নে ও অপরাত্নে নিদ্রা যান। কদাপি গুহা হইতে বাহির হন। প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিশ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া আমাকেই সংগ্রহ করিতে হয়। রাত্রিকালে বিশাল কেশযুক্ত কতিপয় অতিকায় তিব্বতী কুক্কুরী গুহামুখ আগলাইয়া রাখে। ইহারা রাত্রি দ্বিপ্রহর হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত অবস্থান করে। ইহাদের চক্ষু হইতে ভীতিকর নীলাভ শিখা বিচ্ছুরিত হয়। ইহাদের সুদীর্ঘ ও শক্তিশালী দন্তসারি দূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয়।
এ রূপে ছয়মাস অতিবাহিত হইল। আকাশে চাঁদ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে হইতে বৃষের শিঙের আকার ধারণ করিলে ওই বিশেষ নিশিতে গুরুদেবের মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়। গুরুদেব তখন আভূমি নত হইয়া মহাপ্রভুর চরণ চুম্বন করেন। অতঃপর কক্ষের মধ্যখানে যে ছয়প্রান্ত যুক্ত তারকাটি রহিয়াছে, তাহার কেন্দ্রে মুখমণ্ডল, বক্ষ ও পেট স্থাপন করিয়া পৃষ্ঠদেশ ঊর্ধ্বমুখী রাখেন। সেইক্ষণে তাহার দেহ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়া পাঁচটি শ্বেতকায় পেঁচকে রূপান্তরিত হয়। পেঁচকগুলি গুহামুখ অতিক্রম করিয়া শূন্যে মিলাইয়া যায়। সূর্য উদয়ের পূর্বে ওই পেঁচকগুলি পুনরায় গুহায় ফিরিয়া আসে ও তারকাটির উপর উপবেশন করে। অতঃপর উহারা পুনরায় গুরুদেবের দেহ ধারণ করে। গুরুদেবকে একদিন প্রশ্ন করিলাম, পেঁচকের রূপ ধারণ করিয়া গুরুদেব কোথায় গমন করেন? গুরুদেব উত্তর করিলেন, মানবদেহ পাঁচটি বস্তু দ্বারা নির্মিত। উহারা হইল: ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম। সুদীর্ঘ সাধনার পর সিদ্ধিলাভ হইলে মানবদেহ এই পাঁচটি ভাগে বিভক্ত হইয়া যে-কোনও রূপ ধারণ করিতে পারে। আমি পেঁচকের রূপ ধারণ করিয়া আরব উপকূলের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে যে স্থলে প্রাচীন উবার নগরী অবস্থিত ছিল, সে স্থানে গমন করি। অত্র দেশে সহস্রাদি পূর্বে সাদ-বিন-আদ নামক জনৈক সম্রাট দেবাদিদেব আহুরার সম্মানে এ জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্দিরটি নির্মাণ করেন। কালের প্রবাহে সেই স্থাপত্য আজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেও ইহার ভূগর্ভস্থ উপাসনা গৃহ এখনও অতীত গৌরবে সমুজ্জ্বল। এই গর্ভগৃহেই মহাপ্রভু আহুরা তাঁহার প্রিয় তান্ত্রিক-পূজারীদিগের সহিত মিলিত হন এবং হাস্যরসে কালাতিপাত করেন। অপূর্ব দেহবল্লরীসম্পন্ন রমণীগণ তাহাদিগকে সোমরস পান করান। মহাপ্রভু আহুরা তাহাদিগকে ভূত-ভবিষ্যতের কথা বর্ণনা করেন এবং সপ্ত আকাশের অশ্রুতপূর্ব রহস্যময় বিষয়ে কথা বলেন।
এইরূপে একাদশ মাস অতিক্রান্ত হইল। আরও একমাস অতিবাহিত হইলে আমি বরেন্দ্রের উদ্দেশে যাত্রা করিব। গুরুদেব আমার মনোবাঞ্ছা সম্যক উপলব্ধি করিলেন। তিনি এক দিবসে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন: বস, সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে অন্যূন বিশ বৎসরাধিককাল একাগ্র চিত্তে উপাসনার প্রয়োজন। কাপালিক সাধকেরা নানারূপ অপদেবতার সাধন ভজন করিয়া থাকে। এইসব অপদেবতারা সবাই মহাপ্রভু আহুরার দাসানুদাস। এই সকল দেবদেবী নিচু স্তরের বলিয়া ইহাদের বুদ্ধিবৃত্তিও অতি নীচ। ইহারা প্রায়শই রক্তলোভী হইয়া থাকে। কাপালিকেরা ইহাদের তুষ্টি সাধন লক্ষে নরহত্যা ও অন্যান্য ঘৃণ্য পাপাচারে লিপ্ত হয়। তদু। এইসব কাপালিকেরা মরণশীল এবং মৃত্যুর পর ইহারা ওহ সকল অপদেবতার আজ্ঞাবহ হয়। মহাপ্রভু আহুরার উপাসনায় শীলাদেবী ও তদীয় ভ্রাতা পরশুরাম সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন না। উহারা বিষয়ভোগী এবং তাঁহাদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটিয়াছে।
যদি ত্যাগ তিতিক্ষা থাকে, যদি এই জন্যে বাঁচিয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সকালে সিদ্ধি লাভ করিবে। অন্যথায় কালের আবর্তে তুমি পুনঃপুনঃ জন্মলাভ করিতে থাকিবে এবং এক সময় পূর্ব জন্মের স্মৃতি জাগরিত হইলে সেই ক্ষণে সিদ্ধি লাভ করিবে।
এক দিবসে গুরুদেব নগরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আমাকে রাখিয়া গেলেন একাকী গুহায়। মহাপ্রভু আহুরার উদ্দেশে নিয়মিত পূজা-পাঠ করিবার পুনঃপুনঃ কঠোর নির্দেশ দিলেন। গুরুদেবের নির্গমনের পর পঞ্চদশ দিবস অতিক্রান্ত হইল। আমি একাকী গুহায় রহিলাম। রাত্রি দ্বিপ্রহরে কুকুরীসমূহ আসিয়া গুহামুখ আগলাইয়া রাখে। নিদারুণ আতঙ্কের মধ্য দিয়া আমার সময় কাটিতে লাগিল। ষষ্ঠদশ দিবসে বেলা দ্বিপ্রহরে গুরুদেব এক অনন্যসুন্দরী রমণী ও দশজন নেপালী শেরপা সমভিব্যাহারে প্রকাণ্ড একটি সবুজাভ প্রস্তর নির্মিত আধার লইয়া গুহামুখে প্রবেশ করিলেন। এই গুহাটির অদূরে আরও একটি গুহা ছিল। সেই গুহাটিতে সারি সারি সাতটি প্রকোষ্ঠ ছিল। উহার একটিতে গুরুদেব ও অন্যটিতে আমি নিদ্রা যাইতাম। অন্যগুলোতে বস্ত্র এবং আহারের সরঞ্জামাদি ছিল। গুরুদেবের নির্দেশে ইহারই একটি আমি ওই রমণীর জন্য নির্ধারিত করিলাম। ইহার পর গুরুদেব প্রস্তর নির্মিত আধারটির ঢাকনা উত্তোলন করিলে উহার অভ্যন্তরে এক মৃতা তরুণীকে শায়িতাবস্থায় দেখিলাম। মৃতার গাত্রবর্ণ ঘোর কৃষ্ণকায়। গুরুদেব বলিলেন, অপঘাতে মৃত্যু হইয়াছে এমন একজন কুমারী তরুণীর শব ইহা।
অতঃপর গুরুদেব মৃতা তরুণীর শরীরে চন্দন তৈল উত্তমরূপে মালিশ করিলেন। দুর্বোধ্য ভাষায় ক্রমাগত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে গোলাপের নির্যাস জলে মিশ্রিত করিয়া ওই জল দ্বারা শবাধারটি পূর্ণ করিলেন এবং শবাধারটি প্রভু আহুরার পদতলে স্থাপন করিলেন। দেখিতে দেখিতে তরুণীর ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেহ নীলবর্ণ ধারণ করিল। তরুণীর আঁখি পল্লব প্রস্ফুটিত হইল এবং গুরুদেবের সহিত দৃষ্টি বিনিময় ঘটিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তরুণীর অক্ষিপট নিমীলিত হইল। যুবতী রমণী ও আমি যুগপৎ গুরুদেবকে তাহার সাধনার কাজে সাহায্য করিতে লাগিলাম। ক্রমে ক্রমে যুবতীর সহিত আমার সখ্য গড়িয়া উঠিল। বাস্তবিক আমি উক্ত রমণীকে প্রাণাধিক প্রণয় করিতাম। এরূপে দ্বাদশ দিবস অতিক্রান্ত হইলে গুরুদেব সন্নিকটে আহ্বান করিয়া মধুর কণ্ঠে কহিলেন, বৎস, এক্ষণে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন কর। শীলাদেবীর পারিষদদিগের হইতে সাবধানে থাকিবে। উহারা তোমার প্রাণনাশের কারণ হইতে পারে। এ স্থলে যাহা দেখিয়াছ, তাহা স্মরণ রাখিয়ো এবং সাক্ষাৎ ঘটিলে শীলাদেবীকে বিধৃত করিয়ো৷ লিখিবার সরঞ্জাম লইয়া আইস। উপাসনার নিমিত্ত সমস্ত খুঁটিনাটি বিধৃত করিতেছি। লিখিয়া লও! আশীর্বাদ করি। তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক।
বজ্ৰযোগীর বর্ণনা এখানেই শেষ। এরপর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা শুধু বিভিন্ন গাছ-গাছড়া ও ভেষজ উপাদানের নাম ও পরিমাণ ইত্যাদি লেখা। জটিল সব নক্সা আঁকা। বিভিন্ন মাস-দিন তারিখ-গ্রহ-নক্ষত্রের পূর্ণাঙ্গ অপূর্ণাঙ্গ চিত্র এবং প্রাচীন কালের হরফে লেখা অসংখ্য সাঙ্কেতিক চিহ্ন।
স্ক্রলের শেষ পাতার সাথে আটকানো অবস্থায় বৃন্দাবন ঘটকের একটি চিঠি পেলাম।
শুক্রবার। ১৩ আগস্ট
প্রিয়বরেষু শ্রীমান ফারাবী,
আপনার সাথে দেখা হওয়া কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয়। আমি জানতাম আপনি এখানে আসবেন এবং আপনার সাথে দেখা হবে। এজন্যেই পালি ভাষার পাণ্ডুলিপিটা সাথে করে এনেছিলাম। আমি ইতিহাসের অধ্যাপক হলেও আপনার মত এত হাই প্রোফাইল গবেষক নই। আশা করি আপনার গবেষণার কাজে এই পাণ্ডুলিপি সহায়ক হবে।
সেই যে ছোটবেলায় চিত্রকূটের সাথে দেখা হলো, এরপর সে আর কখনও আমাকে ছেড়ে যায়নি। আমাকে সব বিপদ আপদ থেকে রক্ষা তো করেছেই, তার ওপর ভবিষ্যতে কী ঘটবে সেকথাও মাঝে মধ্যে জানিয়েছে। সিধু জ্যাঠা বিশ্বাস করতেন আমিই অতীতের বজ্ৰযোগী।
জীবদ্দশায় বজ্ৰযোগী সিদ্ধি লাভ করতে পারেনি। সে পুণ্ড্রনগরে ফিরে আসার আগেই পরশুরামের পতন ঘটে। করতোয়া নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে শীলাদেবী। কংস সেন তখন পুণ্ড্রনগরের শাসনকর্তা। শীলাদেবীর অনুসারীরা তার প্রাণনাশ করতে পারে এই ভয়ে তটস্থ কংস। সেইসব অনুসারীদের খুঁজে খুঁজে বের করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে তার গুপ্তচর বাহিনী। সব দেখেশুনে মুষড়ে পড়ে বজ্ৰযোগী। সে চলে আসে রামপুর বোয়ালিয়ায় তার বাবার কাছে। গাঁয়ের এককোণে ছোট্ট এক বাড়িতে বজ্রযোগীর বাবা তখন মৃত্যু শয্যায়। বাবার ইচ্ছে, ছেলের বিয়ে দিয়ে পুত্রবধূ দেখে যাওয়ার। কনের খোঁজ পাওয়া গেল, লগ্নও নির্দিষ্ট হলো। বিয়ের কেনাকাটা করতে বজ্ৰযোগী গেল পুণ্ড্রনগরে। তখনকার দিনে এই এলাকায় ওটাই ছিল সবচেয়ে বড় বাজার। বজ্ৰযোগীর দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, ওদিনই ছিল কংসের রাজসূয় যজ্ঞ। কংস বেরিয়েছে সাধারণ নাগরিকদের। সুবিধা-অসুবিধার কথা জিজ্ঞেস করতে। নগরীর পথে পথে হেঁটে বেড়াচ্ছে সে। তার নিরাপত্তার বিষয়টি দেখার জন্যে প্রকাশ্য অ-প্রকাশ্য সব বাহিনীর লোকেরা অবস্থান নিয়েছে। শহরের মোড়ে মোড়ে। ভারতের অন্যান্য সব সমৃদ্ধ নগরীর মতই পুণ্ড্রনগরী ছিল অনেক উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। নগরীতে প্রবেশ এবং নির্গমনের গেট একটাই। কেনাকাটা করে মাল সামান নিয়ে বেরুনোর সময় ধরা পড়ে গেল বজ্ৰযোগী। রাজদ্রোহিতার অভিযোগ এনে সাতদিনের ভেতর শিরচ্ছেদ করা হলো তার। বজ্ৰযোগীর সাধনার ইতি সেখানেই।
এরপর পেরিয়ে গেল শতাব্দীর পর শতাব্দী। সিধু জ্যাঠার মতে বজ্ৰযোগীর পুনর্জন্ম হলো এবং এ জন্মে সে হলো বৃন্দাবন ঘটক অর্থাৎ আমি। সিধু জ্যাঠা আমাকে তান্ত্রিকতা শিক্ষা দিয়েছেন বছরের পর বছর, প্রস্তুত করেছেন চূড়ান্ত পরিণতির জন্যে। সব থেকে বড় কথা, আমি যে এ জন্মের বজ্ৰযোগী একথা উনি বিশ্বাস করিয়েছেন আমাকে। আপনি হয়তো ভাবতে পারেন, ভবিষ্যই যদি দেখতে পাই, তা হলে সিধু জ্যাঠাকে সাবধান করিনি কেন? সিধু জ্যাঠা ভারতে পালিয়ে যাওয়ার সময় ওঁকে বলেছিলাম তার সামনে খুব বড় বিপদ, আরও কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে। কিন্তু ওঁকে তখন যমে টানছে, আমার কথা শুনবেন কেন? বিয়ে করতে নিষেধ করেছিলেন সিধু জ্যাঠা। কিন্তু বাবা-মায়ের মুখ চেয়ে আমাকে ওই কাজটি করতে হয়েছিল। অতি দুর্ভাগ্য, আমার স্ত্রীর গর্ভাবস্থায় এক্লেমশিয়ায় মা-শিশু দুজনেরই মৃত্যু হয়। এরপর ও-রাস্তা আর মাড়াইনি কখনও।
আমি নিশ্চিত তিব্বতে গেলে চিত্রকূটের সাধন পীঠ এখনও খুঁজে পাওয়া যাবে। আর যদি সাধনা ঠিকমত করতে পারি, তা হলে সিদ্ধিও লাভ হবে। তান্ত্রিকদের একটি অন্যতম দায়িত্ব হলো যোগ্য একজন অনুসারী রেখে যাওয়া। এই দায়িত্বটি আপনাকেই দিয়ে যেতে চাই। যে কলেজে চাকরি করতাম, সেখানে আমার বাড়িটি দান করে দিয়েছি। আগামী মাস থেকে ওটা ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহার হবে। সাধনার সমস্ত পুঁথিপত্র, উপাচার দুটো ট্রাঙ্কে ভরে কলেজের প্রিন্সিপালের জিম্মায় রাখা আছে। আপনি গিয়ে চাইলেই ওগুলো যাতে আপনাকে দিয়ে দেয়া হয়, এমত নির্দেশ দিয়ে রেখেছি। আপনার কাছে এসব খুবই আজগুবি মনে হতে পারে। তবে আমি নিশ্চিত, আপনি পুরো বিষয়টি একবার হলেও ট্রাই করে দেখবেন। এত নিশ্চিত হলাম কীভাবে সেটা বলি।
আপনার বাঁ হাতের কব্জির নিচে একটি লাল জড়ল আছে, এটি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন। ঠিক এরকমই একটি জড়ল সিধু জ্যাঠার হাতেও দেখেছি। এটিও হয়তো খেয়াল করেছেন যে খুব বড় বিপদ থেকেও অতি সহজেই রক্ষা পেয়ে যান আপনি এবং অদৃশ্য কেউ সবসময় আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসে। প্রথম যেদিন আপনার সাথে দেখা হয়, সেদিনই মনে হয়েছে আপনার মত একজনকেই খুঁজছি আমি। আগ বাড়িয়ে আপনাকে অতকিছু তখন শোনানোর উদ্দেশ্য ওটাই। তখন থেকেই অপেক্ষা করেছি সঠিক সময়ের।
আন্তরিক শুভ কামনা রইল।
ইতি
বৃন্দাবন ঘটক
দশ
চিঠিটা পড়ে বৃন্দাবন ঘটককে অদ্ভুত এক মানসিক রোগী বলে মনে হলো। ছোটবেলা থেকেই সিধু জ্যাঠা না কে তারমধ্যে এক অবসেশনের জন্ম দিয়েছে। বয়েস বাড়ার সাথে-সাথে সেই অবসেশন এখন হয়ে গেছে ম্যানিয়া। তবে একথা ঠিক যে এই পাণ্ডুলিপির অ্যান্টিক ভ্যালু এবং ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসীম। ঠিক এই জিনিসটাই আমাকে ধন্দে ফেলেছে। সেমিনার শেষ হয়েছে, কালকেই ঢাকা ফিরে যাব। আজকে সারাদিন তেমন কোনও কাজও নেই। এখান থেকে বিড়ালদাহ ত্রিশ মাইলের বেশি হবে না। একবার গিয়ে দেখলে হয়। যদি দুটো ট্রাঙ্ক বৃন্দাবন ঘটক সত্যিই রেখে যান, তা হলে ওখানে মধ্যযুগীয় পুঁথিপত্র আরও অনেক থাকতে পারে।
বিড়ালদাহ পৌঁছে দেখলাম কলেজ বন্ধ। দারোয়ানের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে প্রিন্সিপালের বাসায় গেলাম। প্রিন্সিপাল মনে হলো আমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন। বৃন্দাবন ঘটক নাকি তাকে বলে গেছেন আমি আজই তাঁর সাথে দেখা করব। কলেজ থেকে ট্রাঙ্ক দুটো বাসায় এনে রেখেছেন উনি। আমার জন্যে খাবার দাবারেরও আয়োজন করেছেন। বললেন, এত বড় স্কলার আপনি। আফসোস। কলেজ বন্ধ, তা না হলে আপনাকে দিয়ে একটা লেকচার দেয়াতাম। ছেলেমেয়েরা কিছু শিখতে পারত। তার ওপর আপনি বৃন্দাবন ঘটকের গেস্ট। আপনি হয়তো জানেন না উনি এই এলাকার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় একজন ব্যক্তি।
বিকেলের দিকে একটা রিকশা ভ্যানে ট্রাঙ্ক দুটো উঠিয়ে। বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে রওনা করিয়ে দিলেন প্রিন্সিপাল সাহেব। ভ্যানের সামনের দিকে ট্রাঙ্ক রেখে পেছনের দিকে পা ঝুলিয়ে বসলাম আমি। বিদায় নিয়ে অনেকটা পথ চলে এসেছি। সামনেই একটা মোড় যেখানে ছোট রাস্তা হাইওয়েতে উঠেছে। এমন সময় লক্ষ করলাম, খুব জোরে সাইকেল চালিয়ে ষোলো-সতেরো বছর বয়সের একটি ছেলে আমাদের দিকে ছুটে আসছে। এক হাতে সাইকেলের হ্যাঁণ্ডেল ধরা, অন্য হাতে কাঠের ছোট একটা বাক্স। ভ্যানের চালককে ভ্যান থামাতে বললাম। ঘ্যাচ করে ব্রেক কষে চালক ভ্যান থামাল। হাইওয়ে আর ছোট রাস্তার বর্ডার লাইনে। ভ্যান এত দ্রুত থেমে যাবে সেটি সাইকেল চালক বুঝতে পারেনি। সাইকেল থামাতে-থামাতে সে পৌঁছে গেল ভ্যানের সামনের চাকা থেকে আরও দুফুট দূরে। সাইকেল চালককে চিনতে পারলাম। প্রিন্সিপাল সাহেবের বড় ছেলে এটি। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় রাজশাহী বোর্ড থেকে স্ট্যাণ্ড করেছে। ছেলেটি কাঠের বাক্সটা ভ্যান চালকের হাতে দিয়েছে, ঠিক সেই মুহূর্তে মোড় নিল বড় একটি বাস। সাইকেলসহ ছেলেটাকে চিড়েচ্যাপ্টা করে বেরিয়ে গেল। দুএক পল এদিক ওদিক হলে সাইকেলের জায়গায় থাকার কথা ছিল ভ্যানটার!
বৃন্দাবন ঘটক ট্রাঙ্কের সাথে কাঠের ছোট বাক্সটিও আমার জন্যে রেখে গিয়েছিলেন। প্রিন্সিপাল সাহেব আমাকে ওটা দিতে বেমালুম ভুলে যান। আমাকে বিদায় দিয়ে ঘরে ফিরলে তার স্ত্রী ওটার কথা মনে করিয়ে দেন তাকে। তিনি তৎক্ষণাৎ বাক্সটা তার ছেলের হাতে দিয়ে বলেন আমার কাছে পে দেয়ার জন্যে। ঘটনার দুদিন পরে ঢাকায় ফিরে খুললাম বাক্সটা। দেখলাম ভেতরে লাল ভেলভেটে মোড়ানো লম্বা, সরু একটা কোদাল!