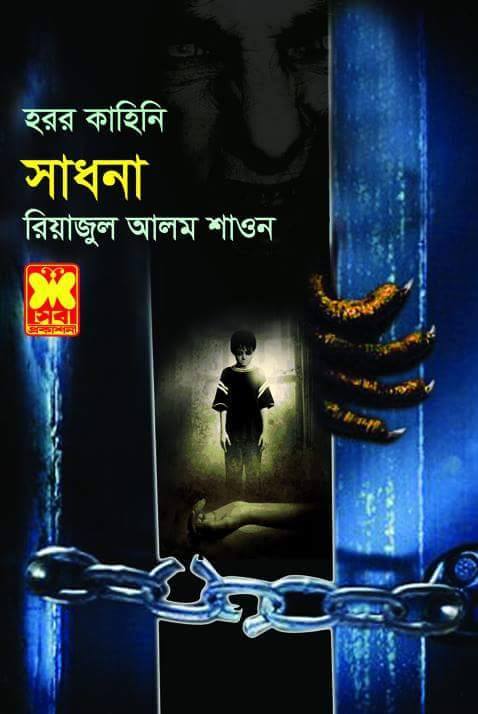- বইয়ের নামঃ সাধনা
- লেখকের নামঃ রিয়াজুল আলম শাওন
- সিরিজঃ সেবা হরর সিরিজ
- প্রকাশনাঃ সেবা প্রকাশনী বই
- বিভাগসমূহঃ ভূতের গল্প
সাধনা
খান্নাস
এক
‘এই, বড্ড ঠাণ্ডা লাগছে! জানালাটা বন্ধ করে দাও,’ সেজানের দিকে তাকিয়ে বলল রেহানা।
‘ঠাণ্ডা লাগছে! কী বলছ পাগলের মত!’
‘হ্যাঁ, খুব ঠাণ্ডা লাগছে।’
‘গরমে অতিষ্ঠ হয়ে গেলাম। ইলেক্ট্রিসিটি নেই দুই ঘণ্টা। আর তুমি বলছ ঠাণ্ডা লাগছে?’
‘আমার মনে হয় জ্বর আসছে।’
‘কই, দেখি।’ সেজান রেহানার কপালে হাত রাখল। শরীর ঠাণ্ডা। জ্বরের ছিটেফোঁটাও নেই।
‘তোমার তো জ্বর নেই।’
‘তুমি প্লিজ জানালাটা বন্ধ করে দাও।’
বিরক্তমুখে জানালা বন্ধ করল সেজান। সেজান-রেহানার বিয়ে হয়েছে আড়াই মাস হলো। সেজানদের পাশের গ্রামের মেয়ে রেহানা। বয়স এখনও আঠারো হয়নি। দেখতে অস্বাভাবিক সুন্দর। এই জন্য সেজান বিয়ের ব্যাপারে খুব আগ্রহী ছিল। সে একটা কোম্পানিতে মার্কেটিং এগযেকিউটিভ হিসাবে কাজ করে। দেখতেও খুব সুদর্শন নয়। এমন সুন্দর মেয়ে বিয়ে করা তার চিন্তার বাইরে ছিল। তবে বিয়ের পর রেহানার আচরণে খুব বিরক্ত সেজান। আজব এক মেয়েকে বিয়ে করেছে ও। সারাদিন ঘরের জানালা-দরজা বন্ধ করে বসে থাকে। কথায়-কথায় বলে, ঠাণ্ডা লাগছে। রাতের বেলা লাইট জ্বেলে ঘুমাতে যায়। লাইট ছাড়া ঘুমাতে নাকি তার আতঙ্ক লাগে। বিয়ের প্রথম থেকেই সেজান লক্ষ করেছে, শারীরিক সম্পর্কের ব্যাপারগুলোতে আগ্রহী নয় রেহানা। রান্না-বান্নাও ঠিকমত পারে না। সবসময় নিজের মনে থাকতে পছন্দ করে। সেজানের সাথে কথাবার্তাও বিশেষ বলে না। তবে রেহানার একটা ভাল দিক আছে। ও ঝগড়া করতে পারে না। তাই সেজান কোনও রূঢ় কথা বললেও চুপচাপ শোনে রেহানা।
ওরা যে বাড়িতে থাকে, তা শহরের একদম শেষ মাথায়। আশপাশে বেশি বাড়ি-ঘর নেই। বাড়ি ভাড়াও খুব বেশি নয়। এমন একটা বাড়িতে বসবাস করা ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু রেহানার এই বাড়ি ভাল লাগছে না। সে বারবার সেজানকে বাসা বদলে ফেলার কথা বলছে। পছন্দসই নতুন বাসা খুঁজে পাওয়া কত কঠিন, সে সম্পর্কে রেহানার কোনও ধারণা নেই। তাই সেজান ওর কথা কানে তুলছে না।
হঠাৎ চমকে উঠে রেহানা বলল, ‘জানালায় কেমন একটা শব্দ হলো না?’
‘বাতাসে শব্দ হয়েছে মনে হয়।’
‘ওই যে, আবারও হলো।’
‘আরে, তোমাকে নিয়ে ভারি মুশকিল হলো দেখি। চুপচাপ ঘুমাও।’
‘আমার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।’
‘মানে?’ সেজান দেখতে পেল রেহানা হাঁ করে শ্বাস নিচ্ছে। দ্রুত জানালা খুলে দিল সে। বাইরের বাতাস ঘরে ঢুকলে হয়তো ওর একটু ভাল লাগবে।
রেহানা চেঁচিয়ে উঠে বলল, ‘তুমি জানালার কাছে যেয়ো না! প্লিজ জানালার কাছে যেয়ো না!’
‘কেন?’
‘ওখানে কেউ দাঁড়িয়ে আছে।’
‘তোমার কি মাথা খারাপ হলো? কে দাঁড়িয়ে থাকবে? আর দোতলায় জানালার ওদিকে দাঁড়ানোর কোনও জায়গা আছে?’
‘আমি জানি, ও আছে।’
‘কে আছে, বলো তো?’
‘না, কেউ না।’
এমন সময় শুরু হলো ঝোড়ো বাতাস। মনে হচ্ছে কেউ যেন প্রচণ্ড আক্রোশে আঘাত করছে জানালায়। কবাট পুরোপুরি খুলে গেল। পুরো ঘর একটু পর-পর কেঁপে উঠতে লাগল। ইলেক্ট্রিসিটি ছাড়াই হঠাৎ ঘুরতে শুরু করল ফ্যানটা। প্রথমে আস্তে-আস্তে, তারপর তুমুল গতিতে। সেজানের মনে হলো, যে-কোনও সময় ভেঙে পড়বে ফ্যানটা। দ্রুত উঠে বসল সেজান। ওকে জড়িয়ে ধরে আছে রেহানা। ওর চোখ বন্ধ। শরীরটা কাঁপছে। রেহানা কাঁপা স্বরে বলল, ‘তুমি উঠো না, প্লিজ উঠো না।’
সেজানেরও কেমন যেন ভয়-ভয় লাগছে।
রেহানা আবার বলল, ‘চোখ বন্ধ করে রাখো। বন্ধ করে রাখো। ভয়…ভয় লাগে…’
সেজান চোখের সামনে তীব্র আলোর এক ঝলকানি দেখল। টায়ার পোড়া গন্ধের মত বিশ্রী গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে। ঘরের কোনায় থাকা চেয়ারটা উল্টে পড়ল মেঝেতে। আরও বেড়ে গেল ফ্যানের গতি। ঝোড়ো বাতাসটাও তীব্র থেকে তীব্রতর হলো। উড়ছে টেবিলের উপর রাখা কাগজগুলো। এমন সময় বিকট শব্দ করে মেঝেতে পড়ে গেল ফ্যানটা। ঘরের ভিতর কারা যেন থপথপ করে হাঁটছে। রেহানাকে জড়িয়ে ধরে আছে সেজান। রেহানার মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে ফেনা। এমন সময় চলে এল ইলেক্ট্রিসিটি। স্তিমিত হয়ে এল ঝোড়ো বাতাসটা।
সেজানের গলা শুকিয়ে গেছে। পিপাসায় যেন ফেটে যাচ্ছে বুক। কিন্তু তবুও বিছানা থেকে নামার সাহস হচ্ছে না। রেহানার জ্ঞান নেই। বিছানায় এলিয়ে পড়ে আছে ওর দেহটা। সেজান দেখতে পেল, রক্ত ঝরছে রেহানার নাক দিয়ে। তেমন কোনও বাতাস নেই ঘরে। তবু উড়ছে ওর চুলগুলো। কী করবে বুঝতে পারল না সেজান। এমন সময় ঘরের বাল্বের দিকে চোখ গেল ওর। বাড়তে লাগল বাল্বের উজ্জ্বলতা। একসময় উজ্জ্বলতা যেন সর্বোচ্চ সীমায় পৌছে গেল। ঘুরতে শুরু করেছে মেঝেতে পড়ে থাকা ফ্যানটাও। ফটাস শব্দে ফেটে গেল বাল্বটা। মুহূর্তেই অন্ধকার হয়ে গেল পুরো ঘর। অন্ধকারেই সেজানের মনে হলো আস্তে-আস্তে উপরে উঠছে ফ্যানটা। একসময় ওর মাথার একটু উপরেই স্থির হলো। নড়ারও সাহস পেল না সেজান। ও একচুল নড়লেই ক্ষতবিক্ষত হবে ফ্যানের পাখায়। ওর নিঃশ্বাস যেন আটকে গেছে। কেউ যেন ওকে বোঝাতে চাইছে, চাইলেই তোমাকে মারতে পারি আমি, কিন্তু করুণা করে তোমাকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছি। আবারও আলোর ঝলকানি দেখতে পেল সেজান। কেমন যেন এক ঘোরের মধ্যে চলে গেল ও।
দুই
ভয়াবহ জণ্ডিসে আক্রান্ত হয়েছে আনোয়ার। হাতের তালু, চোখসহ শরীরের বিভিন্ন অংশ গাঢ় হলুদ বর্ণের হয়ে গেছে। ঘণ্টায়-ঘণ্টায় বমি করছে সে। বড় এক ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছে ওকে। ওর খালাতো বোন নাদিয়া ওর দেখাশোনা করছে। নাদিয়ার মা নার্গিস জাহানও মেয়ের সাথে থাকছেন মাঝে-মাঝে। নার্গিস জাহান আনোয়ারের মায়ের ছোট বোন। নাদিয়ার যখন জন্ম হলো, তখন থেকে তাঁর মনে প্রবল ইচ্ছা আনোয়ারের সাথে মেয়ের বিয়ে দেবেন। নিজের বোনকে মনের কথাটা জানিয়েছিলেন তিনি। আনোয়ারের মা-ও সানন্দে রাজি ছিলেন। কিন্তু আনোয়ার ক্লাস নাইনে পড়ার সময়ে ওর মা মারা যান। নাদিয়া তখন ক্লাস থ্রির ছাত্রী। বোন মারা যাওয়ার পর নার্গিস জাহানের ইচ্ছাটা গোপনই থেকে যায়।
আনোয়ারের বাবা আর বিয়ে করেননি। তিনি আনোয়ারকে নিজের মত করে বড় হতে দিয়েছেন, একই সাথে দিয়েছেন অবাধ স্বাধীনতা। এ জন্য ছেলেটা কেমন যেন অন্যরকম হয়ে গেছে। ঘর-বাড়ি ছেড়ে প্রায়ই বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ায়। ভূত-প্রেতের সন্ধান করে। মাস্টার্স পাশ করে চাকরির কোনও চেষ্টাও করছে না। চেহারায় একটা পাগলের ভাব চলে এসেছে। তাই নার্গিস জাহান এখন আর আনোয়ারের সাথে মেয়ের বিয়ে দিতে তেমন আগ্রহী নন। তবে আনোয়ারের প্রতি তিনি আগের মতই প্রবল মমতা বোধ করেন। সপ্তাহে একদিন আনোয়ারকে না দেখে তিনি থাকতে পারেন না। তিনি যখন আনোয়ারের বাবার কাছে শুনলেন আনোয়ার ক্লিনিকে ভর্তি হয়ে আছে, কেঁপে উঠেছে তাঁর বুকটা। মেয়েকে নিয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ ক্লিনিকে ছুটে এসেছেন। তাঁর মেয়ে নাদিয়া আনোয়ারের সেবা- যত্নের জন্য কষ্টের চূড়ান্ত করছে। নার্গিস জাহানের মনে সন্দেহ জেগেছে যে, নাদিয়ার হয়তো আনোয়ারের প্রতি এক ধরনের দুর্বলতা রয়েছে। এই বয়সে মেয়েরা ভুল মানুষকে পছন্দ করে বসে।
আনোয়ার চোখ মেলে তাকাল। রহস্যের সন্ধানে সারা দেশ ঘুরে বেড়ায় সে। বিষয়টা ধীরে-ধীরে পরিণত হয়েছে তীব্র নেশাতে। রাঙামাটির এবারের ট্যুরটা কঠিন ছিল ওর জন্য। খাওয়া-দাওয়া, ঘুমের ঠিক ছিল না। মাথার উপর ছিল কড়া রোদ। হেপাটাইটিস ভাইরাসটা শরীরে হয়তো অনেকদিন ধরেই বাসা বেঁধে ছিল। এবার সে তার চূড়ান্ত রূপ দেখাল।
আনোয়ারের সামনে সব কেমন যেন হলুদ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে, সে যেন হলুদ সর্ষে খেতের মধ্য দিয়ে হাঁটছে। বহুদূরে একটা মেয়েকে দেখতে পেল সে। মেয়েটার পরনে সবুজ শাড়ি। হলুদের মধ্যে সবুজটা দেখতে ভালই লাগছে।
মেয়েটা হঠাৎ বলল, ‘আনোয়ার ভাইয়া, আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন?’
আনোয়ার হাসার চেষ্টা করল। ‘হ্যাঁ।’
‘বলুন তো আমি কে?’
‘তুমি কেয়া।’
‘ভুল বললেন। আমি কেয়া নই। নাদিয়া। আপনার খালাতো বোন।’
‘ও। হ্যাঁ, তুমি নাদিয়া। চিনতে পেরেছি।’
‘বলুন তো আমি কী পড়ছি?’
‘তুমি এবার এস.এস.সি. দিয়েছ।’
‘না। আমি এবার অনার্স সেকেণ্ড ইয়ারে। আচ্ছা থাক, আপনার আর কথা বলার দরকার নেই। আপনি চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকুন। আমি আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি।’
‘ছোটবেলায় আমি তোমার একটা পুতুল ভেঙে ফেলেছিলাম। তুমি খুব কেঁদেছিলে।’
‘সে তো অনেক আগের কথা।’
‘শাড়িতে তোমাকে সুন্দর লাগছে।’
‘আনোয়ার ভাই, প্লিজ, আর কথা বলবেন না। আমি শাড়ি পরিনি। সালোয়ার-কামিজ পরে আছি।’
একটু পর ডাক্তার দেখতে এল আনোয়ারকে।
ডাক্তারদের চোখ-মুখ সাধারণত অনুভূতিশূন্য হয়। কিন্তু এই ডাক্তারের চেহারা তেমন নয়।
ডাক্তার নাদিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘রোগীর তো নিজেকে নিয়ে কোনও চিন্তা আছে বলে মনে হয় না। লিভারের কণ্ডিশন খুব খারাপ।’
নাদিয়া থতমত খেয়ে বলল, ‘কী বলছেন এসব?’
ডাক্তার আনোয়ারের ফাইলটা দেখতে-দেখতে বলল, ‘এখন থেকে খুব নিয়ম মেনে চলতে হবে। খাবার-দাবার, চলাফেরায় খুব সচেতন থাকতে হবে। পাঁচ দিন আগে যখন আনোয়ার সাহেবকে ক্লিনিকে ভর্তি করা হলো, আমরা তো তাঁকে নিয়ে বেশ ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। এখন অবস্থা কিছুটা উন্নতির দিকে।’
নাদিয়ার ভয়ার্ত চোখ একটু স্বাভাবিক হয়ে এল।
ডাক্তার আবার বলল, ‘নিয়ম মেনে না চললে এই জণ্ডিস বারবার ফিরে আসবে। এরপর হয়তো আমাদের কিছু করার থাকবে না। এমনকী লিভার সিরোসিস বা লিভার ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে।’
আনোয়ার মন দিয়ে ডাক্তারের কথা শুনছিল। লোকটার কথার মধ্যে কোথায় যেন একটু মায়ার ছোঁয়া আছে। সে চোখ মেলে বলল, ‘ডাক্তার সাহেব, আমার কিছু হবে না।
ডাক্তার ধমক দিয়ে বলল, ‘আপনি চুপ করুন। আর একটু হলে তো মরতে বসেছিলেন। শরীরের যত্ন নিতে শিখুন।’
আনোয়ার হাসার চেষ্টা করল।
ডাক্তার বলল, ‘আপনি কী করেন, জানতে পারি?’
‘আমি আসলে বেকার। দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে সময় কাটাই।’
‘পর্যটক?’
নাদিয়া বলল, ‘আনোয়ার ভাই রহস্য, ভূত-প্রেত এসবের সন্ধানে ঘুরে বেড়ান। বিভিন্ন ধরনের মন্ত্র, দোয়া-দরূদ তাঁর মুখস্থ।’
ডাক্তার চোখ কপালে তুলে বলল, ‘বলেন কী? …আচ্ছা, আনোয়ার সাহেব, ভূত বলে সত্যি কিছু আছে? আপনি কি কখনও দেখেছেন?’
আনোয়ার আবার হাসল। বুঝিয়ে দিল তার উত্তর দেয়ার ইচ্ছা নেই।
‘শুনুন, আনোয়ার সাহেব, ভূতের পিছনে ছোটা বাদ দিয়ে একটা চাকরি করুন। একটা ভাল মেয়েকে বিয়ে করুন। আবার অনিয়ম করলে কিন্তু আপনি মারা যাবেন। কে জানে, হয়তো ভূতই হয়ে যাবেন। হা-হা-হা!’
এই লোকের হাসিটা প্রাণখোলা। ডাক্তারের এমন প্রাণখোলা হাসি দেখলে অর্ধেক সুস্থ হয়ে যায় রোগী।
ডাক্তার চলে যাওয়ার পর আনোয়ারকে স্যুপ খাইয়ে দিতে শুরু করল নাদিয়া।
আনোয়ার লজ্জিত গলায় বলল, ‘আর দিয়ো না। বমি আসছে। শেষে হয়তো দেখা গেল তোমার গায়ে বমি করে দিয়েছি।
নাদিয়া বলল, ‘গত পাঁচ দিনে আপনি আটবার আমার গায়ে বমি করেছেন। আরও একবার করলে সমস্যা নেই।’
আনোয়ার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ডাক্তার সাহেবের কথা হঠাৎ ওর মাথায় চেপে বসল। নাদিয়ার মত এক মেয়েকে বিয়ে করলে মন্দ হয় না।
তিন
সেজান পাশের ফ্ল্যাটের রহমত আলীর ঘরে বসে আছে। চোখ-মুখ শুকনো। বুকের ভিতরটা কোনও কারণ ছাড়াই টিপ-টিপ করছে। মাথার চাপা ব্যথাটা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে।
সেজানকে দেখে রহমত আলী বলল, ‘কী, সেজান সাহেব, কেমন আছেন?’ তার কথা বলার ভঙ্গিতে আন্তরিকতা টের পাওয়া যায়। মধ্যবয়স্ক রহমত আলীর মুখ সদা হাস্যময়। সেই মুখে রাগ বা দুঃখের ছাপ সহজে ফুটে ওঠে না। মুখের বিশ্রী বসন্তের দাগ আর অস্বাভাবিক ছোট চোখ ধূর্ত ভাব নিয়ে এসেছে তার চেহারায়। তার দিকে বেশি সময় তাকিয়ে থাকলে সেজানের কেমন যেন অস্বস্তি হতে থাকে।
সেজান রহমত আলীর দিকে না তাকিয়ে উত্তর দিল, ‘জী, ভাল আছি।’
‘মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে না, খুব ভাল আছেন।’ সবকিছু বুঝে ফেলেছেন এমনভাবে কথাগুলো বলল রহমত আলী।
‘আসলে একটা কথা জানার জন্য আপনার কাছে এসেছিলাম।’
‘বলুন।’
‘ইয়ে, মানে কাল রাতে আমাদের ইলেক্ট্রিসিটি লাইনে কিছু সমস্যা হয়েছিল। বাল্ব ফেটে গেছে। ফ্যানটা নীচে ভেঙে পড়েছে।’
‘বলেন কী! কালকে রাতে অবশ্য ভোল্টেজ আপ-ডাউন করেছে অনেকবার। আমাদের এই বাড়িতে কারেন্টের লাইনে বেশ সমস্যা আছে।’
‘কাল রাতে হঠাৎ ঝড় শুরু হলো, তখন…
সেজানকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করে বসল রহমত আলী, ‘আজব কথা! ঝড় আবার কখন হলো?’
‘না-না, ঠিক ঝড় না, ঝোড়ো বাতাস।’ নিজেকে সামলে নিয়ে কথাটা ঘুরিয়ে নিল সেজান।
‘ঝোড়ো বাতাস হয়েছে নাকি? টের পাইনি তো!’
‘আচ্ছা, আমি উঠি।’ চোখে-মুখে অনিশ্চয়তার ভাব নিয়ে উঠে পড়ল সেজান।
‘আরে, বসুন। চা খেয়ে যান। আপনার ভাবী অবশ্য ছেলেমেয়ে নিয়ে কয়েকদিনের জন্য বাপের বাড়িতে গেছে। তাই আমাকেই চা বানাতে হবে।’
‘চা খাব না।’
‘বুঝতে পেরেছি। নতুন বিয়ে তো। ভাবীকে অল্প সময় না দেখলেই অস্থির লাগে, না?’ চোখ দিয়ে অশ্লীল এক ইঙ্গিত করল রহমত আলী।
‘না। বাসায় যাব না। অফিসে যেতে হবে।’
‘আরে, মিয়া, শুধু অফিস-অফিস করেন কেন! আসল অফিস তো বাড়িতেই। বউয়ের সাথে গুর মত সবসময় আটকে থাকবেন। হা-হা-হা!’ একতরফা হাসিটা বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলল।
সেজান উঠে দাঁড়াল। অফিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে তার।
.
রেহানা বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। গতরাতের কথা কিছু মনে করতে পারছে না শুধু চাপা আতঙ্ক চেপে আছে তার বুকে। সকালে মিস্ত্রি ডেকে এনে ফ্যান লাগিয়েছে সেজান। নতুন বাল্বও লাগানো হয়েছে। যদি ফ্যানটা তাদের মাথার উপর ভেঙে পড়ত, তা হলে কী ভয়ঙ্কর কাণ্ডই না ঘটত। কেন এমন হচ্ছে, কিছুটা আন্দাজ করতে পারছে রেহানা। ডায়রিতে সে তার জীবনের কিছু অন্যরকম ঘটনা লিখে রেখেছে। প্রায়ই ইচ্ছা হয় কেউ ডায়রিটা পড়ুক। রক্ষা করুক তাকে বিপদ থেকে। সেজানকেও বারবার কথাগুলো বলতে ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলা হয়নি। নিজের জীবনে ওকে জড়িয়ে মস্ত বিপদের মধ্যে পড়ে গেছে বেচারা।
বারান্দা থেকে ফিরে গোসল করতে বাথরুমে ঢুকল রেহানা। পানির স্পর্শটা খুব ভাল লাগল। গ্রামে থাকতে ছোটবেলায় প্রায়ই নদীতে সাঁতার কাটত। বাথরুমে চোখ বন্ধ করে সেই মজার দৃশ্যটা দেখতে চেষ্টা করল রেহানা। সে যেন ঢাকা শহরের বদ্ধ কোনও বাথরুমে নয়, বরং গ্রামের সেই নদীতে আছে।
ডোরবেল বেজে উঠল। একবার নয়, দু’বার নয়, পরপর তিনবার। রেহানা ভেজা কাপড় ছেড়ে শুকনো পোশাক পরল। শরীরে ওড়না জড়ানোর বা চুলগুলো ভাল করে মোছার সময় পেল না। আবারও তিনবার বেজে উঠল ডোরবেল। দরজাটা অল্প একটু ফাঁক করে গলাটা বের করে বলল রেহানা, ‘কে?’
রহমত আলীকে দেখা গেল। হাসিমুখে সে রেহানার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ভাবী, আমি। দরজাটা খুলুন। আপনার ভাবী আমাকে পাঠিয়েছে। আপনার সাথে একটু দরকার আছে।’
রেহানা দরজা খুলবে কি না এক মুহূর্ত ভাবল। এরপর দরজা খুলে দিল। রহমত সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘আপনি সোফাতে বসুন। আমি আসছি।’
‘ভাবী, একটু পরে যান। আমি বেশি সময় নেব না।’ রেহানার পুরো শরীরে ঘুরতে থাকে রহমত আলীর দৃষ্টি।
ভেজা চুল। এলোমেলো পোশাক। ফর্সা দেহ। উচ্ছল যৌবন।
নিজেকে যেন ধরে রাখতে পারল না রহমত আলী। ইচ্ছা করছে ঝাঁপিয়ে পড়তে মেয়েটার উপর। রহমত আলী বুঝে-শুনেই এই সময়ে এসেছে। সেজান বাসায় নেই। আর পাশাপাশি ফ্ল্যাট হওয়াতে কেউ গোসল করতে ঢুকলেই পাওয়া যায় পানির শব্দ। রহমত কান পেতে ছিল কখন বাথরুমে ঢুকবে রেহানা। অল্পবয়সী এই মেয়েটাকে গোসলের পরে দেখার দারুণ ইচ্ছা ছিল তার।
‘বলুন, কী বলবেন,’ মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল রেহানা।
‘কালকে রাতে আপনাদের ফ্যান ভেঙে পড়েছে শুনলাম। বাল্বও নাকি ফেটে গেছে। আপনি ঠিক আছেন কি না তা-ই দেখতে এলাম।’ কথা বলতে-বলতে উঠে দাঁড়াল রহমত আলী।
রহমত আলীর দিকে তাকাল রেহানা। আস্তে-আস্তে ওর দিকে এগিয়ে আসছে রহমত আলী। সড়াৎ শব্দে টেনে নিল সে জিভের লালা। ‘ভাবী, আপনার তো এখন আনন্দের সময়। মজা আর উপভোগের সময়। আপনার জামাটা মনে হয় একটু টাইট হয়ে গেছে, না?’
রেহানা চমকে উঠল।
রহমত এখন তার আরও কাছে।
ভয়ে মুখ সাদা হয়ে গেল রেহানার। বলল, ‘আপনি আর কাছে আসবেন না।’
‘ভাবী, মনটা বড় করতে শিখুন। জীবনকে উপভোগ করতে শিখুন। আমার কিন্তু টাকার অভাব নেই।’
‘আর কাছে আসবেন না!’
তবু এগিয়ে যেতে লাগল রহমত। রেহানা মেয়েটাকে আজ সে কিছুতেই ছাড়বে না।
এমন সময় অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটল। টায়ার পোড়া গন্ধে পুরো ঘর ভরে উঠল। কেউ যেন মুহূর্তেই শূন্যে তুলে নিল রহমতকে। এরপর ছুঁড়ে দিল দেয়ালের দিকে। প্রচণ্ড আঘাত লাগল রহমতের কাঁধে, পিঠে এবং কোমরে। ঘরে কী ঘটল বুঝতে পারল না রহমত। কোনওমতে উঠে দাঁড়াল। রেহানার শরীর সোফার উপর এলিয়ে পড়ে আছে। মুখ দিয়ে বেরোচ্ছে ফেনা। মনে হচ্ছে জ্ঞান নেই। প্রচণ্ড ব্যথা অগ্রাহ্য করে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গেল রহমত আলী। পুরো পৃথিবীটা দুলছে তার চোখের সামনে। সে বের হওয়ার সাথে-সাথে কেউ ধড়াম করে বন্ধ করে দিল রেহানাদের দরজাটা।
চার
দশ দিনের মাথায় ক্লিনিক থেকে রিলিজ করে দেয়া হলো আনোয়ারকে। এখন অনেকটাই সুস্থ সে। তবে আগামী এক মাস বাইরে বের হওয়া তার জন্য নিষেধ। এ ছাড়া, মশলা জাতীয় খাবার আপাতত হারাম। নিয়মিত পানি ফুটিয়ে খাওয়ারও পরামর্শ দিয়েছে ডাক্তার।
নার্গিস জাহান আনোয়ারকে নিয়ে এসেছেন নিজ বাসায়। আনোয়ারের বাবা প্রথমে রাজি হতে চাইছিলেন না। কিন্তু আনোয়ারের এখন দরকার পূর্ণ যত্ন। আর নিজ বাড়িতে সেবা করার মত কেউ নেই। এই যুক্তির কাছে আনোয়ারের বাবা পরাজিত হয়েছেন। তিনি ব্যবসার কাজে সবসময় ব্যস্ত থাকেন। মাসের মধ্যে একবার তাঁকে দেশের বাইরেও যেতে হয়। তাই নার্গিস জাহানের কাছেই ছেলেকে ছেড়ে দিয়ে কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করছেন তিনি। প্রতিদিন একবার এসে দেখে যান ছেলেকে।
নাদিয়ার শরীরের উপর দিয়ে এই কয়েকদিন অনেক ধকল গেছে। এখন আনোয়ারের অবস্থা অনেক ভাল। তার দায়িত্ব অনেক কমেছে। তাই অনেকদিন পর সে দশ ঘণ্টার টানা ঘুম দিল। জেগে উঠে দ্রুত ফ্রেশ হয়ে নিল। আজ দোতলার রেহানার কাছে যাওয়ার ইচ্ছা তার। মেয়েটাকে ওর খুব পছন্দ। কী সাধাসিধে মিষ্টি মেয়ে। সেজান এবং রেহানা এই বাসায় এসেছে দুই মাস হলো। দুই মাসেই রেহানার সাথে চমৎকার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে নাদিয়ার। দোতলার অন্য ফ্ল্যাটের রহমত সাহেব নাকি অসুস্থ। তাঁকেও দেখতে যাওয়া উচিত। তাঁর নাকি সমস্যা হয়েছে মেরুদণ্ডের হাড়ে। তিনি এখন মোটামুটি শয্যাশায়ী। তাঁর স্ত্রী মোরশেদা গতকাল কাঁদতে-কাঁদতে নাদিয়াকে বলেছে, ‘কী যে হলো মানুষটার! আমি বাচ্চাদের নিয়ে একটু বাপের বাড়ি গিয়েছিলাম। এর মধ্যে একদিন উনি বাথরুমে পড়ে যান। কাঁধ, পিঠ এবং কোমরে খুব আঘাত পেয়েছেন। ডাক্তার বলল, মেরুদণ্ডে নাকি সমস্যা। এখন পুরো শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। বিছানা থেকে ঠিকমত উঠতেও পারেন না।’
.
রেহানাদের বাসার দরজার সামনে এসে দাঁড়াল নাদিয়া।
দরজা খুলতে অনেক দেরি হলো রেহানার। আজকাল দরজা খুলতে কেমন যেন আতঙ্ক লাগে। সেদিন রহমত আলী বাসায় আসার পর যেসব ঘটনা ঘটেছিল, কাউকে সেসব বলেনি। সেজানকেও না।
রেহানার দিকে তাকিয়ে নাদিয়া বলল, ‘এই, কী হয়েছে তোমার? শরীর খারাপ নাকি?’
‘না, আপা। শরীর খারাপ না।’
‘ভাল কোনও সুসংবাদ আছে নাকি?’
রেহানা লজ্জা পেল। বলল, ‘কী যে বলেন, আপা। এত তাড়াতাড়ি না।’
‘থাক-থাক, আর লজ্জা পেতে হবে না। তুমি তো এই কয়েকদিনে অনেক শুকিয়ে গেছ। কোনও বিষয় নিয়ে চিন্তায় পড়ে গেছ নাকি?’
‘তেমন কিছু না, আপা।’ কথা বলার সময় হতাশাটা লুকাতে পারল না রেহানা।
‘বুঝতে পারছি তোমার একান্ত ব্যক্তিগত কোনও বিষয়। আমি অন্যের গোপন কথা শুনতে চাই না। তবে কোনও বিষয়ে সাহায্য লাগলে আমাকে বলবে। আমি ভাল পরামর্শ দিতে পারি।’
‘জী, আপা, অবশ্যই বলব,’ শুষ্ক গলায় বলল রেহানা।
রেহানার সাথে বেশ কিছুক্ষণ গল্প করে চলে এল নাদিয়া। বুঝতে পেরেছে, রেহানা কোনও সমস্যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বাচ্চা মেয়ে। কিন্তু এত অল্প বয়সেই সংসারের দায়িত্ব কাঁধে নিতে হয়েছে। কে জানে, হয়তো স্বামীর সাথে মানিয়ে চলতে পারছে না।
.
নাদিয়া চলে যাওয়ার পর ভয়ের ভাবটা ফিরল রেহানার। সেজান কখন যে বাসায় আসবে! ওকে নিয়ে খুব বিপদে পড়েছে মানুষটা। প্রায়ই আজব সব ব্যাপার ঘটছে ঘরে। সেদিন সেজান নিজ থেকেই বলল, ‘বাসাটা ভাল না। ভাবছি নতুন বাসায় উঠব।’
রেহানা সম্মতিসূচক মাথা নেড়েছে। সে মুখ ফুটে বলতে পারেনি যে, বাসা বদলালেও কাজ হবে না কোনও। হয়তো একমাত্র রেহানার মৃত্যুই সব ঠিক করতে পারে। আচ্ছা, নাদিয়া আপাকে কি সব বলা যায়? আপাকে দেখলে কেমন যেন একটু ভরসা হয়। আর আপা সাহায্য করতে পারুক বা না পারুক, সব জানলে হয়তো ওর পাশে থাকবেন। নাকি আপার আবার কোনও বিপদ হবে?
রেহানা ঠিক করল, ওর ডায়রিটা দিয়ে আসবে আপাকে। ওটা পড়লেই ওর সমস্যা সম্পর্কে জানা যাবে।
পাঁচ
নাদিয়ার রুমে বসে আছে রেহানা।
ওকে একগাদা খাবার খেতে দিয়েছে নাদিয়া। খুব মজা করে আপেল খাচ্ছে রেহানা। দৃশ্যটা দেখতে ভাল লাগছে নাদিয়ার।
ওর দিকে তাকিয়ে রেহানা বলল, ‘আপা, আমি আসলে অনেক বড় বিপদে আছি। কেন জানি আপনাকে সব বলতে ইচ্ছা করছে।’
‘অবশ্যই বলবে। আমি মন দিয়ে তোমার কথা শুনব।’
‘মুখে বলব না, আপা। আমার এই ডায়রিটা পড়ুন। আমার সমস্যাটা এই ডায়রিতে লিখে রেখেছি।’
এমন সময় ঘরে ঢুকল আনোয়ার। তাকে দেখে কিছুটা বিব্রত হলো রেহানা। ভালভাবে শরীরে জড়িয়ে নিল ওড়নাটা। আজকাল পুরুষ মানুষ দেখলেই কেমন যেন অস্বস্তি লাগে।
নাদিয়া বলল, ‘রেহানা, উনি আনোয়ার ভাই। আমার খালাতো ভাই। তাঁকে এত লজ্জার কিছু নেই। আর, আনোয়ার ভাই, ও রেহানা। দোতলায় থাকে।’
রেহানার দিকে তাকিয়ে হাসল আনোয়ার। তারপর বলল, ‘নাদিয়া, তোমরা কথা বলো। আমি ছাদে যাচ্ছি।’
‘আচ্ছা, আনোয়ার ভাই।’
কিছুক্ষণ পর চলে গেল রেহানা।
রেহানার ডায়রি পড়তে শুরু করল নাদিয়া।
আমার নাম রেবেকা আক্তার রেহানা। ছোটবেলা থেকেই রূপগঞ্জ গ্রামে আমি পরিচিত মুখ। কারণ, আমার নানারকম দুষ্টুমিতে সবাই অতিষ্ঠ ছিল। আমার জন্মের কয়েক মাস আগে বাবা মারা যায়। আর যখন আমার বয়স তিন বছর, তখন আমার মা-ও মারা যায়। মা-বাবা মারা যাওয়ার পর আমার দায়িত্ব গ্রহণ করেন আমার বড় মামা-মামী। এমন মামা-মামী পাওয়ার ভাগ্য খুব কম মানুষেরই হয়। মামার দুই ছেলে-মেয়ে। লায়লা আর কবির। আমার সবসময় মনে হত, মামা-মামী নিজ সন্তানের চেয়েও আমাকে বেশি ভালবাসতেন।
মামার একমাত্র মেয়ে লায়লা ছিল আমারই বয়সী। তাই আমার প্রতিটা দুষ্টুমিতে আমার সঙ্গী হত। বিভিন্ন গাছের ফল চুরি, শীতকালে খেজুরের রস চুরি, সমবয়সী ছেলে-মেয়েদের সাথে মারামারি ছিল আমাদের নিত্যদিনের কাজ। আমি পড়াশোনায় বেশ ভাল ছিলাম। ক্লাস ফাইভে বৃত্তি পেয়েছিলাম। কিন্তু স্কুলেও আমার দুষ্টুমিতে সবাই অতিষ্ঠ ছিল। নানা কারণে প্রতিদিন লোকে মামা-মামীর কাছে নালিশ নিয়ে আসত। কিন্তু মামা-মামী আমাকে কখনও বকতেন না। তাঁদের অতিরিক্ত আদর পেয়ে আমি যেন আস্ত একটা বাঁদর হয়ে উঠলাম।
আমি তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। আমি আর লায়লা ঠিক করলাম সোবহান কাকাদের খেজুর গাছের রস চুরি করব। কিন্তু ওই সময় আমি বড় হচ্ছি, আগের মত বাচ্চা নেই। তাই যখন-তখন বাসা থেকে বের হওয়া আমার জন্য নিষেধ ছিল। বুঝতে পারলাম, কাজটা করতে হবে অতি গোপনে। তা ছাড়া, সোবহান কাকা ছিলেন বদরাগী ধরনের মানুষ। তিনি আমাদের ধরতে পারলে কপালে দুঃখ আছে।
রাত দশটায় লায়লার আর আমার বের হওয়ার কথা। কিন্তু ওই সময় হঠাৎ লায়লা বলল, ওর ভয় লাগছে। ও আজ যাবে না। আমাকেও যেতে নিষেধ করল।
আমি বুঝতে পারলাম, ওর ঘুম পাচ্ছে। তাই অজুহাত দিচ্ছে। আমি রাগত গলায় বললাম, ‘তুই না গেলে আমি কিন্তু একাই যাব।’
লায়লা হাই তুলতে-তুলতে বলল, ‘সাহস থাকলে একা যা।’
লায়লা জানে রাতে একা রস চুরি করার মত দুঃসাহস আমার হবে না। কিন্তু আমার জেদ চেপে গেল। তাই একা-একাই বেরিয়ে পড়লাম। অন্ধকার রাত। পোকা-মাকড় শব্দ করছে একটানা। আমি বারবার চমকে উঠছি আর পিছনে তাকাচ্ছি। বারবার মনে হচ্ছে কেউ যেন আমার পিছনে-পিছনে আসছে।
সোবহান কাকাদের অনেকগুলো খেজুর গাছ। আমি খুব ভাল গাছে চড়তে পারি। রস খাওয়ার ইচ্ছা তেমন একটা ছিল না। কিন্তু রস চুরি করে লায়লাকে বীরত্ব দেখানোর ইচ্ছাটা পেয়ে বসেছিল।
আমি একটা গাছে উঠতে শুরু করলাম। উঁচু গাছ। উঠতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। কিছুদূর ওঠার পর আমার মনে হলো, আশপাশের পরিবেশ হঠাৎ অস্বাভাবিক রকম শান্ত হয়ে গেল। নীচে নেমে যাব কি না ভাবছিলাম, কিন্তু একটু অপেক্ষা করে আবার উপরে উঠতে শুরু করলাম। এমন সময় হঠাৎই দেখতে পেলাম, আমার ঠিক মাথার উপরে একজন মানুষ। সে উল্টোভাবে গাছে ঝুলে আছে। তার গায়ে কোনও কাপড় ছিল না। দেখলাম তার সারা শরীরে অসংখ্য ছোট-ছোট গর্ত। সেই গর্তে সাদা-সাদা পোকা ঘুরে বেড়াচ্ছে। মনে হচ্ছে পোকাগুলো যেন লোকটার শরীরে বাসা বানিয়ে নিয়েছে। তার চোখ নেই। চোখের কোটরও পোকায় পরিপূর্ণ। লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে বিশ্রীভাবে হাসল। মুখের মধ্যেও পোকা ভর্তি অনেকগুলো ছোট-ছোট গর্ত দেখতে পেলাম। লোকটা হিসহিসে গলায় বলল, ‘রস খাবা?
আমি মৃগী রোগীর মত কাঁপতে লাগলাম। একসময় বুঝতে পারলাম, নীচে পড়ে যাচ্ছি। কয়েক মুহূর্তেই নীচে পড়ে জ্ঞান হারালাম। শব্দ আর চিৎকার শুনে সোবহান কাকাদের ঘর থেকে অনেকেই বের হলো। তারা আমাকে মামার বাসায় নিয়ে গেল। বেশ উপর থেকে পড়ার পরেও আমার শরীরে আঘাত খুব বেশি লাগেনি।
মাথায় পানি ঢালা হলো। একসময় আমার জ্ঞান ফিরল। কিন্তু সেটা পূর্ণ জ্ঞান ফেরা নয়। ধীরে-ধীরে একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেলাম। আশপাশের সবকিছু কেমন যেন ছায়া-ছায়া মনে হচ্ছিল।
প্রচণ্ড জ্বর এল আমার। যাকে বলে আকাশ-পাতাল জ্বর। মামা-মামী গ্রামের ডাক্তার-কবিরাজ কোনোটাই বাদ রাখলেন না। কিন্তু আমার জ্বর কমল না। আমাকে শহরের হাসপাতালেও নেয়া হলো। সেখানে অনেক পরীক্ষা করেও ডাক্তাররা কোনও রোগ খুঁজে পেলেন না। তিন দিন পর আমাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেয়া হলো। এর মধ্যে আমি অনেকবারই ওই লোকটাকে দেখতে পেয়েছি। এমনকী তার শরীরের পোকাগুলোও স্পষ্ট দেখেছি। লোকটাকে দেখলেই আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। আর জ্ঞান হারালেই আমার মুখ দিয়ে বেরোতে থাকে ফেনা।
হাসপাতাল থেকে ফেরার পর অনেকেই বলল, আমার উপর নাকি জিনের আছর হয়েছে। আমাকে তাই লোকমান ফকিরের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো। লোকমান ফকির সুফি ধরনের মানুষ। সারাদিন ইবাদত-বন্দেগির মধ্যে থাকেন। সবাই তাঁকে পবিত্র মানুষ মনে করে। তিনি নাকি মানুষের চোখ দেখে অনেক কিছু বলে দিতে পারেন। আমাদের গ্রামসহ আশপাশের অনেক গ্রামে তাঁর বিশেষ পরিচিতি ছিল। তাঁর নাকি জিন সাধনাও আছে।
আশপাশের পাঁচ-দশ গ্রামে কাউকে জিনে ধরলে একমাত্র ভরসা লোকমান ফকির। তিনি কোরআনে হাফেজ। কিন্তু নামের প্রথমে কখনও হাফেজ টাইটেল ব্যবহার করেন না। তাঁর তিন কুলে কেউ নেই। অল্প বয়সে বিয়ে করেছিলেন। সেই স্ত্রী বিয়ের এক বছরের মাথায় কলেরায় মারা যায়। এরপর আর বিয়ে করেননি। বাড়িতে একা-একাই থাকেন। তাঁর বাড়ি নিয়ে গ্রামে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। খুব দরকার না পড়লে কেউ ওই বাড়িতে যেতে চায় না।
লোকমান ফকির কোনও শারীরিক অসুস্থতার চিকিৎসা করেন না। শুধুমাত্র জিনে ধরা রোগীদেরই চিকিৎসা করেন। এর বিনিময়ে অল্পবিস্তর হাদিয়াও গ্রহণ করেন। তবে কেউ কিছু না দিলে কখনও আপত্তি করেন না।
আমাকে দেখলেন লোকমান ফকির। দেখে তাঁর মুখ কালো হয়ে গেল। আমার কপালে হাত রাখলেন। মুখে বিষাদের ছায়া পড়ল।
মামার দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘মেয়েটার ভাগ্য খুব খারাপ। মনে হচ্ছে ওকে বাঁচানো কঠিন হবে।’
মামা কাঁদো-কাঁদো মুখে বললেন, ‘এসব কী বলছেন?’
‘খারাপ এক জিনের কবলে পড়েছে মেয়েটা। জিনটা মুক্তি দিতে না চাইলে মেয়েটা বাঁচবে না।’
মামা হাত জোড় করে বললেন, ‘আপনি ওকে বাঁচান, হুজুর!’
‘বাঁচানোর মালিক আল্লাহ্ পাক। তবে আমি চেষ্টা করব। জিনটার সাথে কথা বলতে হবে।‘
‘বলুন, হুজুর, কথা বলুন।‘
‘হাবভাবে মনে হচ্ছে, ওর কাছে সবসময় থাকে না জিনটা। মাঝে-মাঝে আসে। তবে আমি এই মুহূর্তেই তাকে ডেকে আনার চেষ্টা করব।’
‘হুজুর, আপনি বললেন, জিনটা সবসময় রেহানার সাথে থাকে না। তা হলে সবসময় এত অসুস্থ হয়ে আছে কেন, হুজুর?’
‘এই খারাপ জিনের নানাবিধ ক্ষমতা আছে। প্রথম দিনেই ও রেহানার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। ওর সেই খারাপ শক্তির প্রভাবে শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েছে মেয়েটা। আমার ধারণা জিনটা কিছু চায়। সেটা পেলে হয়তো ওকে ছেড়ে দেবে। আমি একটু কথা বলার চেষ্টা করতে চাই। মেয়েটাকে রেখে আপনারা চলে যান।‘
‘আমরা বাইরে অপেক্ষা করি।’
‘না, আপনারা বাড়িতে যান।‘
মামাসহ আরও বেশ কয়েকজন লোকমান ফকিরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।
লোকমান ফকির চোখ বন্ধ করলেন। এরপর জোরে জোরে দোয়া-দরূদ পড়তে শুরু করলেন। একসময় এল জিনটা। তখন আমি পুরোপুরি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। মুখ দিয়ে বেরোতে লাগল ফেনা। জিনের সাথে লোকমান ফকিরের বেশ কিছু কথা হলো।
জিন প্রথমে এসে লোকমান ফকিরকে সালাম দিল
লোকমান ফকির সালামের উত্তর দিলেন।
লোকমান ফকির বললেন, ‘তুই কে?’
‘আমি খান্নাস।’
‘খান্নাস তুই!’
‘জী, হুজুর। আমি খান্নাস। বহু বছর ধরে আমি আপনার অধীনে আছি।’
‘মেয়েটাকে কষ্ট দিচ্ছিস কেন? তোর মতলব কী?’
‘মেয়েটাকে আমি পেতে চাই।’
‘না। এটা কখনোই সম্ভব নয়।
‘হুজুর, তা হলে মেয়েটাকে আমি মেরে ফেলব।’
‘আমি তোকে কষ্ট দেব। তুই কিন্তু আমার অধীনস্থ। তোকে আমার কথা শুনতে হবে।‘
‘হুজুর, আমি আপনার কথা শুনব। ওকে সারিয়ে তুলব। ওকে ছেড়ে দেব। তবে…’
‘তবে কী?’
‘আপনাকেও এই গোলামের কিছু কথা শুনতে হবে।’
‘বল, তুই কী চাস।’
‘হুজুর, আপনি আমাকে এই গ্রামে আটকে রেখেছেন। আপনার জন্য আমি ঠিকমত চলাচলের সামর্থ্যও হারিয়েছি। তাই আমাকে আপনার মুক্তি দিতে হবে।’
‘আচ্ছা, যা, তোকে আমি মুক্তি দেব।’
‘শুকরিয়া, হুজুর। আর একটা আর্জি শুনতে হবে, হুজুর।’
‘আবার কী?’
‘মেয়েটাকে আমার পছন্দ হয়েছে। তাই ওকে ভুলতে পারব না। ওকে ছেড়ে যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু ও যেন সারাজীবন চিরকুমারী থাকে। মেয়েটা যদি কখনও বিয়ে করে, তা হলে আমি আবার ওর জীবনে ফিরে আসব।’
‘আচ্ছা, তাই হবে।’
খান্নাস আবারও সালাম দিয়ে বিদায় নিল।
একটু পর আমি চোখ মেলে তাকালাম। আমার জ্বর যেন এক নিমেষে কমে গেছে। মনের ভেতরের চাপা ভয়টাও আর নেই। এতদিন যে ঘোরের মধ্যে ছিলাম, সেই ঘোর থেকেও পুরোপুরি বেরিয়ে এসেছি।
আমি লোকমান ফকিরের দিকে তাকিয়ে বললাম, ‘হুজুর, পানি খাব।’
লোকমান ফকির আমাকে পানি এনে দিলেন। এরপর আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করে দিলেন। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আমি তো ওই সময় ঘোরের মধ্যে ছিলাম। এমনকী অনেক সময় অজ্ঞানও হয়ে যেতাম। তা হলে, লোকমান ফকিরের সাথে জিনের কথোপকথন বা অন্যান্য বিষয় এত বিস্তারিত কীভাবে বর্ণনা করলাম? উত্তরটা সহজ। আমি সুস্থ হওয়ার পর মামা আমাকে সবকিছু বলেছিলেন। প্রথম দিকে তিনিও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কখনও আমার বিয়ে দেবেন না। কিন্তু সময়ের সাথে-সাথে মানুষের ভয় কমে যায়। অতীতকে খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যায় মানুষ।
কয়েক মাস আগে মামা খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। দুই বছর আগে তিনি লায়লার বিয়ে দিয়েছিলেন। তাই আমাকেও বিয়ে দিয়ে চিন্তামুক্ত হতে চেয়েছিলেন। লোকমান ফকিরের নিষেধ মনে করিয়ে দেয়া হলো তাঁকে। কিন্তু তিনি এত আগের বিষয়টার তেমন গুরুত্ব দিতে চাইলেন না।
যথাসময়ে আমার বিয়ে হলো। আমার বর সেজান আমাদের পাশের গ্রামের ছেলে। তারও মা-বাবা কেউ নেই। আপন বলতে এক চাচা। তার চাচার সাথে মামার খুব ভাল বন্ধুত্ব ছিল। তাই বিয়ের কথা পাকা হতে সময় লাগল না।
বরকে আমার খুব পছন্দ হলো। সে যে আমাকে সুখে রাখবে, এ ব্যাপারে আমার কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বাসর রাতেই ঘটল বিপত্তি। সেজান আমার কাছে আসতেই আমার মনে ঘটতে শুরু করল অদ্ভুত কিছু। আবার সেই নগ্ন লোকটাকে দেখলাম। তার শরীরের গর্তগুলো আরও বড় হয়েছে। অসংখ্য পোকা কিলবিল করছে সেই গর্তে। কিছু-কিছু পোকার মুখে আবার ডিম রয়েছে। সেই লোকটা আগের মত আমাকে বলল, ‘রস খাবা?’
আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। মুখ দিয়ে বেরোতে লাগল ফেনা।
এরপর থেকে প্রায়ই ওই লোকটার বেশ ধরে খান্নাস ফিরে আসে। কখনও স্বপ্নে, কখনও-বা তাকে সরাসরি দেখি। খান্নাসের ভাব-ভঙ্গিতে মনে হচ্ছে, সে আমার এবং সেজানের বড় কোনও ক্ষতি করবে। ইতিমধ্যে সে কয়েকবার আমাদের বাসা লণ্ডভণ্ড করেছে। এমনকী নীচে ফেলে দিয়েছে ঘরের ফ্যান। সেজান এসবের কারণ বুঝতে পারছে না। বেচারা খুব কষ্টের মধ্যে পড়েছে। আমি তাকে সবকিছু খুলে বলব ভাবছি। তাকে বলব, আমাকে তালাক দিতে। তা হলে হয়তো সে ওই ভয়াবহ খান্নাসের হাত থেকে মুক্তি পাবে। নিজের জীবন নিয়ে অবশ্য অত ভাবি না। মৃত্যুই আমার একমাত্র মুক্তি।
.
রেহানার ডায়রিটা বন্ধ করল নাদিয়া। বুকের মধ্যে চেপে থাকা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এল তার।
ডায়রিটা নিয়ে আনোয়ারের ঘরে ঢুকল নাদিয়া।
শুয়ে-শুয়ে বই পড়ছিল আনোয়ার। তার শরীর এখনও পুরোপুরি ভাল হয়নি শুয়ে-বসে থাকতে-থাকতে শরীরে যেন মরিচা ধরে গেছে। তবুও সব হাসিমুখে সহ্য করছে আনোয়ার। কারণ সামনে অনেকগুলো জায়গায় ঘুরতে হবে তার। শরীরটা তাই পুরোপুরি ঠিক করা দরকার।
নাদিয়া বলল, ‘আনোয়ার ভাই, আপনার খুব বোরিং সময় কাটছে, না?’
‘না, বোরিং না। আমি আসলে সেবা-যত্ন পেয়ে অভ্যস্ত না। তোমাদের সেবা-যত্নে যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছি। মনে হচ্ছে পরিবার বিষয়টা খারাপ না।’
‘বিয়ে-টিয়ে নিয়ে ভাবছেন নাকি?’
‘একটু-আধটু ভাবছি।’
‘আপনি তো রহস্য-প্রেমিক। কোনও মানবীর প্রেমে কি আপনি পড়বেন?’
‘পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি রহস্য তো লুকিয়ে আছে মানবীর মধ্যেই।’
‘ভাল বলেছেন। আপনি এত সুন্দর করে কথা বলতে পারেন, আগে জানতাম না।’
‘সম্ভবত রূপবতী তরুণীর কাছাকাছি থাকলে সব ছেলেই সুন্দর করে কথা বলার চেষ্টা করে।’
‘আমি রূপবতী? শুনতে ভাল লাগল।’ হেসে ফেলল নাদিয়া।
হাসিতে যোগ দিল আনোয়ারও।
কয়েক সেকেণ্ড পর মুখটা একটু গম্ভীর করে বলল নাদিয়া, ‘আনোয়ার ভাই, এটা রেহানা নামের এক মেয়ের ডায়রি। আমাকে পড়তে দিয়েছে। আমি চাই ডায়রিটা আপনিও পড়ুন। আপনি তো অনেক অতিপ্রাকৃত, ভৌতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন। তাই পুরো ঘটনাটা জেনে আপনার প্রতিক্রিয়া কী হয়, জানতে ইচ্ছা করছে। আপনি নিশ্চয় বিষয়টা আরও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।’
‘অন্যের ডায়রি অনুমতি ছাড়া পড়া কি ঠিক হবে?’
‘আমি রেহানাকে বুঝিয়ে বলব। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, ওর এই ভয়াবহ সমস্যার কোনও সমাধান আপনি দিতে পারবেন।’
‘আচ্ছা, ডায়রিটা রেখে যাও।’
ডায়রিটা রেখে চলে গেল নাদিয়া।
ডায়রির ছোট ওই লেখাটা পড়তে আনোয়ারের লাগল পঁয়ত্রিশ মিনিট। সে আরও দুইবার মন দিয়ে লেখাটা পড়ল। তারপর ব্যস্ত ভঙ্গিতে পরতে লাগল পোশাক।
সুযোগ বুঝে আস্তে-আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল আনোয়ার।
যেতে চায় সে রেহানাদের গ্রামে। ঢাকা থেকে খুব বেশি দূরে নয়। গাড়িতে চার-পাঁচ ঘণ্টা লাগার কথা।
আনোয়ার একটা চিরকুট রেখে গেছে।
নাদিয়া,
জরুরি দরকারে ঢাকার বাইরে যাচ্ছি। চিন্তা কোরো না, দ্রুতই ফিরে আসব। রেহানা মেয়েটার পাশে থেকো। সম্ভব হলে আমার জন্য অপেক্ষা কোরো।
চিরকুটটা যখন পেল নাদিয়া, তখন আনোয়ার গাবতলি বাসস্ট্যাণ্ডে। আনোয়ারকে ফোন করার চেষ্টা করে দেখল, সে ফোনটা বাসায় রেখে গেছে। চোখের কোণে পানি জমল নাদিয়ার। কাঁদতে-কাঁদতে চিরকুটটা বুকে জড়িয়ে ধরল। বিড়বিড় করে বলল, ‘আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করব। সবসময় অপেক্ষা করব।’
ছয়
রূপগঞ্জ যখন পৌঁছাল তখন পার হয়ে গেছে সন্ধ্যা। লোকমান ফকিরের বাড়িটা খুঁজে বের করল আনোয়ার। লোকমান ফকির বেশ অসুস্থ। আনোয়ারকে দেখে তিনি বললেন, ‘আপনি কে?’
‘আমার নাম আনোয়ার। আমি ঢাকায় থাকি।’
‘আমার কাছে কী মনে করে?’
‘আমি আসলে রেহানার ব্যাপারটা নিয়ে আপনার সাথে কথা বলতে চাই,’ কিছুটা ইতস্তত করে বলল আনোয়ার।
রেহানার বিষয়ে? আপনি কথা বলতে এসেছেন!!!’
‘হ্যাঁ। সম্ভবত জিন খান্নাস রেহানার কাছে ফিরে এসেছে।’
দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন লোকমান ফকির, ‘আমি জানতাম ও ফিরে আসবে। রেহানার বিয়ে হলে খান্নাস ওকে ছাড়বে না। আমি ওর মামাকে আগেই সাবধান করেছিলাম। ওরা আমার কথা শুনল না।’
‘রেহানার এখন কী হবে তা হলে?’
‘খান্নাস মেয়েটা এবং তার স্বামীকে মেরে ফেলবে।’
‘আপনি ওদের বাঁচান।’
‘এটা আমার পক্ষে এখন আর সম্ভব নয়। … আপনি রেহানার কে হন?’
‘আমি আসলে রেহানার আপন কেউ নই। অলৌকিক অদ্ভুত বিষয়গুলোর প্রতি প্রবল আকর্ষণ আছে আমার। সেই আগ্রহ থেকেই রেহানার বিষয়টা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। সবকিছু জানার পর রেহানার জন্য কিছু করতে ইচ্ছা হয়েছে।’
‘আপনার চোখ দেখেই আমি অবশ্য বুঝেছি, আপনার মধ্যে আল্লাহ্ প্রদত্ত কিছু শক্তি রয়েছে। আপনার মনোবল অনেক শক্ত। তবে খান্নাসের কাছ থেকে রেহানাকে রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব।’
‘কোনও উপায়ই কি নেই রেহানাকে রক্ষার?’
মুখটা অনেক গম্ভীর হয়ে গেল লোকমান ফকিরের। আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, ‘জিন বিষয়ে কি আপনার কোনও ধারণা আছে?’
‘খুব বেশি কিছু জানি না। আমাকে কি পুরো বিষয়টা একটু বুঝিয়ে বলবেন?’
‘হুম, শুনুন তা হলে। জিন আগুন দিয়ে তৈরি। আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআন মাজিদে সূরা আল হিজরের ২৭ নাম্বার আয়াতে বলেছেন: ‘আর ইতঃপূর্বে জিনকে সৃষ্টি করেছি উত্তপ্ত অগ্নিশিখা থেকে।’ দুষ্ট এবং মন্দ জিনকে আরবিতে বলে ইফরীত। এরা মানুষের ক্ষতি করার জন্য ব্যতিব্যস্ত থাকে। কোনও মানুষেরই উচিত না জিনদের ব্যবহার করে কোনও কাজ সমাধা করা। এতে তাদের সাহস ও ঔদ্ধত্য বেড়ে যায়। তখন তারা মনে করতে শুরু করে, তারা মানুষের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ্ পাকও কোরআন মাজিদে এ সম্পর্কে মানুষকে সাবধান করেছেন। সূরা আল জিনের ছয় নাম্বার আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেছেন: ‘আর নিশ্চয় কতিপয় মানুষ আশ্রয় নিত কতিপয় জিনের, ফলে তারা তাদের অহঙ্কার বাড়িয়ে দিয়েছিল।’ খান্নাস আমার অধীনস্থ ছিল। সত্যি বলতে মন্দ জিনকে অধীনে রাখতে অনেক শক্তি ও সাহসের প্রয়োজন হয়। আলহামদুলিল্লাহ, তার সবই আমার আছে। আমি কখনও খান্নাসের কাছে কোনও বিষয়ে সাহায্য চাইনি। কারণ, এতে করে বেড়ে যেত ওর সাহস। হয়তো একসময় আমার ক্ষতি করারও চেষ্টা করত। ওকে আমি নির্দিষ্ট একটা এলাকার মধ্যে বন্দি করে রেখেছিলাম। খান্নাস তাই পূর্ণ মুক্তি পাওয়ার জন্য ফন্দি করে। একদিন রাতে রেহানাকে একা পেয়ে যায়। রেহানাকে ভয় দেখায়। কেউ ভয় পেলে ইফরীতদের শক্তি বহুগুণে বেড়ে যায়। ভীত মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে ওরা।
‘আমি জিনদের সাহায্য নিতে চাইনি। কিন্তু রেহানাকে বাঁচানোর জন্য আমি খান্নাসের সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছি। এই সুযোগে সে নিজের মুক্তির ব্যবস্থা করে নিয়েছে। এখন আমার আগের সেই মানসিক দৃঢ়তা নেই যে, খান্নাসকে কথা শুনতে বাধ্য করব। তা ছাড়া, আমি এখন বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন অসুখে ভুগছি। প্রায়ই আমার হাত এবং গলা কাঁপতে থাকে। দোয়া-দরূদও ভুলে যাই অনেক সময়। তাই আমি যদি খান্নাসকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হই, তা হলে আমাকে ও মেরে ফেলবে।’
‘আচ্ছা, আমি কি খান্নাসকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারব?’
‘আপনি!’
‘হ্যাঁ। আমি চেষ্টা করতে চাই।’
‘এটা অনেক বড় ঝুঁকির কাজ। খান্নাসকে ডেকে এনে আপনি যদি ওকে নিজের আয়ত্তে না আনতে পারেন, তা হলে কিন্তু মৃত্যু অনিবার্য। আর ভাল মানুষ ছাড়া কেউ এদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।’
‘আমি তবু ঝুঁকিটা নিতে চাই। আর মানুষ হিসাবে আমি একদম খারাপ নই।’
‘আপনাকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে আমার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু অসহায় একটা মেয়েকে সাহায্য করতে চাইছেন বলে, না বলতে পারছি না। আচ্ছা, আপনি শুদ্ধভাবে কোরআন মাজিদ তেলাওয়াত করতে পারেন?’
‘ছোটবেলায় খুব ভালভাবে পারতাম। এখন অনেক নিয়ম-কানুন ভুলে গেছি।’
‘ও, আচ্ছা। একটু বিরতি দিয়ে লোকমান ফকির আবার বললেন, ‘খান্নাসকে ডেকে আনার জন্য আপনি রেহানাদের বর্তমান বাসায় যাবেন। সেই বাসার নির্জন কোনও জায়গা বেছে নেবেন। বাসার ছাদ হলে সবচেয়ে ভাল হয়।’
‘ঘটনাচক্রে আমি এখন রেহানাদের বাসায়ই আছি।’
‘তা হলে তো ভালই। রেহানাদের বাসার নির্জন জায়গায় পাক পবিত্র হয়ে বসে আপনি সূরা জিন পড়া শুরু করবেন। সূরাটা পুরোপুরি মাখরাজ অনুসরণ করে পড়তে হবে। আপনাকে আমি গুন্নাহ, টান সহ কোরআন মাজিদ পড়ার নিয়ম-কানুনগুলো আবার মনে করিয়ে দেব।’
‘জী, অবশ্যই।’
‘সূরা পাঠ ঠিকভাবে করতে পারলে খান্নাস আপনার আশপাশে চলে আসবে কোনও ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে। আপনার একটা জিনিস সবসময় মনে রাখতে হবে, কোনও পরিস্থিতিতেই আপনার ভয় পাওয়া চলবে না। ভয় পেলেই খান্নাস আপনার উপর প্রভাব বিস্তার করবে। আপনাকে মেরে ফেলবে কিংবা আপনার বড় কোনও ক্ষতি করবে। আপনার অবশ্য একটা সুবিধা আছে।’
‘কী সুবিধা?’
‘খান্নাস আসলে অন্ধ।’
‘অন্ধ!’
‘হ্যাঁ। তবে জিনদের গন্ধশক্তি দৃষ্টিশক্তির চেয়েও তীক্ষ্ণ। তাই আপনি ওর সাথে একটা চাতুরি করতে পারেন।’
‘কী চাতুরি?’
‘আমি একটা আতর তৈরি করেছি। একমাত্র আমিই এই আতরটা ব্যবহার করি। গন্ধটা একদম অন্যরকম। এবং এই গন্ধটা খারাপ জিনদের পছন্দ নয়। খান্নাস যখন আমার অধীনে ছিল, তখন সে বলত, এই আতরের গন্ধ শুঁকে সে আমাকে চিনতে পারে। তাই আমি ভাবছি আপনাকে এই আতরটা দেব। আপনি আতরটা মেখে ডেকে আনবেন খান্নাসকে। গন্ধ শুঁকে খান্নাস ভাববে, ওর সামনে বসে আছে লোকমান ফকির। ও আমাকে ভয় পায়। তাই ওকে কথা শোনানো অনেক সহজ হবে। কিন্তু যদি একবার বুঝতে পারে, ওকে ধোঁকা দেয়া হচ্ছে, তবে কিন্তু আরও বাড়বে আপনার বিপদ। আপনি ভয় পেতে শুরু করলেই খান্নাস সত্যটা বুঝে ফেলবে। আবারও বলছি, খান্নাসকে নিয়ন্ত্রণের একটাই উপায়: কোনও অবস্থাতেই ভয় পাওয়া চলবে না।’
‘আমার মধ্যে ভয় জিনিসটা একেবারে কম। জীবনে অনেকবার জীবন-মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়াতে হয়েছে। তাই আমার মনে হয়, আমি পারব।’
‘খান্নাসকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য আরও বেশ কিছু নিয়ম-কানুন মানতে হবে আপনাকে। আজ থেকে নামাজ ঠিকমত পড়বেন, সবসময় পবিত্রতা বজায় রাখবেন। মুখে গন্ধ হয় এমন কিছু খাবেন না। আপনাকে আরও বেশ কিছু দোয়া- দরূদ শিখতে হবে। সূরা জিন সঠিকভাবে তেলাওয়াত শিখতে হবে। তাই আমার মনে হয়, কালকের দিনটা আপনি আমার সাথে থাকলে ভাল হবে।’
‘জী, অবশ্যই।’
‘এখানে আপনার খাবার কষ্ট হবে। আমি দরিদ্র মানুষ। মূলত একবেলা ভাত খাই। আর একবেলা গুড়-মুড়ি। মেহমানকে সেবা করার বিশেষ সামর্থ্য আমার নেই।’
‘আমার কোনও সমস্যা হবে না।’
‘চলুন, এশার নামাজ পড়তে হবে। এরপর ভাত রান্না করব। রাতের খাওয়া শেষে আপনাকে কিছু দোয়া শেখাব। আজ রাতে তাহাজ্জুদের নামাজও পড়তে হবে।’
আনোয়ার মাথা নাড়ল। কেমন যেন ক্লান্তি লাগছে, বমি আসছে।
লোকমান ফকির বলল, ‘আমাকে সবসময় একা থাকতে হয়। সবাই আমাকে ভয় পায়। সবাই ভাবে, আমার বাড়ি হয়তো জিন-ভূতে পূর্ণ। আপনাকে পেয়ে মনে আনন্দ হচ্ছে।’ লোকমান ফকির হাত ধরে আনোয়ারকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। বললেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ, কোনও মানুষকে স্পর্শ করলে বুঝতে পারি, মানুষটা ভাল না মন্দ।’
আনোয়ার হেসে বলল, ‘আমাকে স্পর্শ করে কী মনে হচ্ছে?’
‘আপনি মানুষ হিসাবে অনেক ভাল। আপনার মনে কলুষতা নেই বললেই চলে। তবে আপনি ধর্ম-কর্মের ব্যাপারে বেশ উদাসীন।’
একজন পবিত্র মানুষ যখন এভাবে প্রশংসা করেন, সত্যিই আরও ভাল হতে ইচ্ছা করে। লোকমান ফকির হাসলেন। আনোয়ারের মনে হলো, তাঁর হাসিটাও পবিত্র।
সাত
লোকমান ফকিরের কাছে একদিন নয়, দু’দিন নয়, তিন দিন থাকল আনোয়ার। তিনি আনোয়ারকে ধ্যান করা, শরীর পবিত্র রাখার বিভিন্ন বিষয় শিখিয়ে দিলেন সূরা জিন সহ প্রয়োজনীয় দোয়া-দরূদও সঠিকভাবে পড়ার নিয়ম-কানুন শিখে নিল আনোয়ার। ওর আরবি উচ্চারণ শুনে খুশি হলেন লোকমান ফকির। বললেন, ‘আপনার কোরআন তেলাওয়াত খুব চমৎকার লেগেছে। আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন।’
.
প্রচণ্ড মাথাব্যথা নিয়ে নাদিয়াদের বাসায় ঢুকল আনোয়ার। আনোয়ারকে দেখে চমকে উঠল নাদিয়া। ‘কোথায় গিয়েছিলেন আপনি? নিজেকে কী মনে করেন?’
আনোয়ার উত্তর না দিয়ে হাসল। মেয়েটার রাগ দেখতে ভাল লাগছে। ও শুধু বলল, ‘একটু জরুরি কাজ পড়ে গিয়েছিল।’
‘আপনি কি রেহানাদের গ্রামে গিয়েছিলেন?’ –
‘হ্যাঁ।’
‘মানুষের বিপদ নিয়ে আপনি খুব ভাবেন, না?’
‘চেষ্টা করি। সবসময় তো আর পারি না।’
‘আমাকে তো আপনার মানুষ মনে হয় না।’
‘ছি-ছি, এসব কী বলছ, নাদিয়া?’
‘তা হলে কেন আমার বিপদে পাশে থাকছেন না?’
‘তোমার কী বিপদ?’
‘আপনি চোখের সামনে না থাকলে আমার…’
‘তোমার…’
‘কিছু না।’ আরেক ঘরে চলে গেল নাদিয়া।
নার্গিস জাহানও অনেক বকাবকি করলেন আনোয়ারকে।
নাদিয়া ছাড়া কেউ জানল না আনোয়ার কোথায় গিয়েছিল।
.
রেহানার প্রচণ্ড জ্বর। সব ধরনের টেস্ট করা হয়েছে, কিন্তু খুঁজে পাওয়া যায়নি কোনও রোগ।
রেহানা আবার চলে গেছে ঘোরের মধ্যে। সে এখন নিয়মিত সেই নগ্ন মানুষটাকে দেখতে পায়। মাঝে-মাঝে জ্ঞানও পুরোপুরি হারিয়ে ফেলে। তখন মুখ দিয়ে বেরোতে থাকে ফেনা। সেজানের কেন জানি মনে হচ্ছে, আর বাঁচবে না রেহানা। কষ্টে যেন ফেটে যাচ্ছে তার বুক।
ঘরের ভিতর প্রায়ই অস্বাভাবিক সব কাণ্ড চলছে, যা সেজানকে আরও বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। সেদিন হঠাৎ রান্নাঘরে আগুন লেগে গেল। ভাগ্যিস আগেভাগে দেখেছিল রেহানা। নতুবা ঘটত বড় অঘটন। ঘরের ভিতর প্রায়ই ফেটে যাচ্ছে বাল্ব। কোনও কারণ ছাড়াই যখন-তখন হচ্ছে তীব্র বাতাস। এ ছাড়া, সেদিন দুটো মরা বিড়ালের বাচ্চা পাওয়া গেছে খাটের তলে। আর টায়ার পোড়া গন্ধটা তো আছেই।
এসব ঘটনা বাদেও, দু’দিন আগে এই বাড়িতে আরও একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটেছে। পাশের ফ্ল্যাটের রহমত আলী হঠাৎই মারা গেছে। পচন ধরেছিল তার শরীরে। ফুলে ঢোল হয়ে গিয়েছিল পেট। বিশ্রী কিছু পোকা বাসা বেঁধেছিল শরীরে। কয়েকদিন তীব্র যন্ত্রণা ভোগ করে অবশেষে মারা গেছে রহমত আলী।
সবকিছু মিলিয়ে খুব অসহায় লাগছে সেজানের। সে খবর পাঠিয়ে গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছে রেহানার মামীকে। তিনি রেহানার অবস্থা দেখে অস্থির হয়ে পড়েছেন ভয়ে।
আট
রাত এগারোটার একটু বেশি বাজে। ঘুমিয়ে পড়েছে নাদিয়াদের বাসার সবাই। এখন ছাদে বসে আছে আনোয়ার। ছাদের দরজা বন্ধ করে রেখেছে, যাতে হুট করে কেউ আসতে না পারে ছাদে। এই বাড়ির আশপাশে খুব বেশি লোকবসতি নেই। সেটাও বাড়তি সুবিধা দিচ্ছে আনোয়ারকে।
চুপচাপ হতে শুরু করেছে চারদিক। আজ বেশ জেঁকে বসেছে শীতটা। গায়ে সাদা পোশাক আনোয়ারের। শরীরে শীতের বাড়তি কোনও পোশাক নেই। বেশ কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস রয়েছে আশপাশে: লোহার শিক, মাটির ঢেলা ইত্যাদি। ধ্যানমগ্ন আনোয়ার প্রথমে নানাধরনের দোয়া-দরূদ পড়ে শান্ত করল মনকে। এরপর জ্বালল তিনটা বড় মোমবাতি। বুকের মধ্যে অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছে ওর। সেটা ভয় নয়, শঙ্কা নয়, অন্য কিছু। মোমবাতির আলোতেই সূরা জিন পাঠ করা শুরু করল আনোয়ার এক মনে।
অন্য কোনও দিকে নজর নেই ওর। আস্তে-আস্তে পড়ছে, কিন্তু মনে হচ্ছে, বহুদূর ছড়িয়ে পড়ছে সূরা পাঠের আওয়াজ। নড়ছে গাছের পাতা। মোমবাতির শিখা কাঁপছে মৃদু বাতাসে। যেন অন্য জগতে চলে যাচ্ছে আনোয়ার। কাঁপছে গলা।
চলছে সূরা তেলাওয়াত। চলছে…চলছে…
সূরা তেলাওয়াতের একদম শেষ দিকে হঠাৎ শুরু হলো দমকা বাতাস। একবারে নিভে গেল দুটো মোমবাতি। সেদিকে একটু তাকাল আনোয়ার। তারপর আবার শুরু করল পড়তে। দ্রুত পায়ে ছাদে হাঁটাহাঁটি শুরু করল কেউ। হঠাৎ টায়ার পোড়া গন্ধ পেল আনোয়ার। তারপর কেউ যেন প্রচণ্ড আক্রোশে কিছু ছুঁড়ে দিল ওর দিকে। একটা মরা বিড়াল দেখল আনোয়ার। চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল বিড়ালটার নাড়ি-ভুঁড়ি।
এরপর আনোয়ারের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল কেউ। এখন একটা মোমবাতি জ্বলছে ছাদে। অল্প আলোতে এক মানুষকে দেখতে পেল আনোয়ার। শরীরে তার অসংখ্য গর্ত। সেই গর্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে সাদা-সাদা পোকা। এমন কী চোখের জায়গাটাতেও কিলবিল করছে অসংখ্য পোকা।
খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে বলল, ‘হুজুর, আস্সালামু আলাইকুম।’
‘ওয়ালাইকুম আস্সালাম।’
‘হুজুর, আপনি আমাকে আবার ডেকেছেন কেন?’
ভয়-ভয় লাগছে আনোয়ারের। কেন জানি মনে হচ্ছে, হেরে যাবে সে। ওর জন্য অপেক্ষা করছে নির্মম পরিণতি।
আনোয়ার বলল, ‘তুই কেন এসেছিস রেহানার কাছে?’
‘হুজুর, আমি বলেছিলাম, ও বিয়ে করলে ওকে আমি ছাড়ব না।’
‘আমি এখন বলছি, ওকে ছেড়ে চিরতরে চলে যা।’
খান্নাস মাথা নাড়ল। সে যাবে না। কিছুতেই না।
‘খান্নাস, তুই বড়জোর মেরে ফেলবি রেহানাকে। কিন্তু আমিও তোকে ছাড়ব না, সেটা মাথায় রাখিস। আমি আবার তোকে আটকে রাখব। তুই কি তাই চাস?’
‘না-না। আমি মুক্তি চাই। মুক্তি চাই।’
‘তা হলে নিজ দেশে ফিরে যা।’
‘আমি রেহানার কাছে থাকব, হুজুর।’
‘না, তা হবে না। কিছুতেই না,’ কঠোর গলায় বলল আনোয়ার। জোরে- জোরে বেশ কিছু সূরার আয়াত পড়তে লাগল সে। এরপর খান্নাসের দিকে ছুঁড়ে দিল একটা লোহার শিক।
খান্নাস চিৎকার করে উঠল। ‘হুজুর, আমার কষ্ট হচ্ছে!’
‘তুই যদি না যাস, তবে আরও কষ্ট পেতে হবে তোকে।’
আসলে পুরো বিষয়টাই চলছে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে। খান্নাস বিশ্বাস করে ফেলেছে, ওর সামনে লোকমান ফকির বসে আছেন। তিনি বিভিন্ন সূরার আয়াত পড়ে ছুঁড়ে দিতেন লোহার শিক। তাতে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হত খান্নাসের। একইভাবে লোহার শিক ছুঁড়ে দিয়েছে আনোয়ারও।
এখন যদি ভয় পেতে থাকে আনোয়ার, বা এতটুকু ভুল করে, তবে সব শেষ করে দেবে খান্নাস।
বৃত্তাকারে ঘুরতে শুরু করল খান্নাস। বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল শরীরের পোকাগুলো। বড় একটা আগুনের হলকা চলে গেল আনোয়ারের গা ঘেঁষে। আনোয়ারের শরীরে চেপে বসতে চাইল খান্নাস। অশরীরী কোনও শক্তিতে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠল আনোয়ারের কপালের রগ। একইসাথে কেউ যেন জোরে- জোরে আঘাত করতে লাগল মাথায়। দাঁতে দাঁত চেপে নিজেকে স্বাভাবিক রাখল আনোয়ার। চোখের সামনে দেখতে পেল অনেকগুলো ভয়ঙ্কর মুখ, যেসব মুখ এ জগতের কারও নয়। এরপর দেখল কিছু মরা লাশ। কিছু হিংস্র জন্তু খাচ্ছে সেই লাশ, বারবার গর্জন করছে। তবু বিচলিত হলো না আনোয়ার। জানে, সব ভ্রম বা মিথ্যা। ওকে ভয় দেখাতে চাইছে খান্নাস। যদি একটু ভয়ও আনোয়ার পায়, তো ওকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করবে খান্নাস। কিন্তু ভয়ের অনুভূতিটা দূরে ছুঁড়ে ফেলল আনোয়ার। ও মানুষ, সৃষ্টির সেরা জীব। কিছুতেই হারবে না খান্নাসের কাছে।
আনোয়ার এবার দেখতে পেল পুরো ছাদে কিলবিল করছে অসংখ্য পোকা। গুটি-গুটি পায়ে সেগুলো এগিয়ে আসতে লাগল আনোয়ারের দিকে। কিছু-কিছু পোকার মুখে ডিমও দেখা গেল। চোখ বন্ধ করল আনোয়ার। এরপর দুটো ছোট মাটির ঢেলা নিয়ে মুষ্টিবদ্ধ করল দুই হাত। জোরে-জোরে লোকমান ফকিরের শিখিয়ে দেয়া কয়েকটি বিশেষ দোয়া পড়তে লাগল। কিছুক্ষণ পর হাতের মুষ্টি খুলল। ঢেলা দুটো ছুঁড়ে দিল খান্নাসের দিকে।
আক্রোশে দাপাতে লাগল খান্নাস। এক নিমেষে যেন কাঁপিয়ে দিল সে পুরো ছাদটা। ভেঙে চুরমার হয়ে গেল ফুলের টবগুলো। এরপর রাগত গলায় বলল, ‘হুজুর, আমি রেহানাকে ছেড়ে চলে যাব। আমি আর মানব সমাজে আসব না।’
‘কথা দিচ্ছিস?’
‘হ্যাঁ, কথা দিচ্ছি।’
‘আমি আবার চোখ বন্ধ করছি। চোখ খুলে যেন দেখি তুই নেই।’
‘জী, হুজুর। আমি চলে যাচ্ছি। তবে আপনার জন্য কিছু একটা রেখে যাব আমি। অবশ্যই রেখে যাব।’
চোখ বন্ধ করে আছে আনোয়ার। প্রচণ্ড বাতাসে ঠিক রাখতে পারছে না সে নিজেকে। নাড়ি-ভুঁড়ি বের হওয়া মরা বিড়ালটা নড়ে উঠল হঠাৎ। জোরে ডেকে উঠল, ‘মিয়াও!’
বিদ্যুতের ঝলকে যেন আলোকিত হয়ে গেল পুরো আকাশটা। বেশ কিছুক্ষণ পর শান্ত হলো ছাদের পরিবেশ।
আনোয়ার চোখ মেলে দেখল, ওকে ঘিরে আছে অসংখ্য পোকা। সবগুলো যেন ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল একসাথে।
শরীর থেকে পোকাগুলো ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করল আনোয়ার। কিন্তু ওর শরীর আঁকড়ে ধরে রাখল ওগুলো।
নয়
জ্ঞান নেই রেহানার। মুখ দিয়ে ক্রমাগত বেরোচ্ছে ফেনা। বারবার অনিয়ন্ত্রিতভাবে কেঁপেও উঠছে। কিছু যেন কিলবিল করে ছুটে বেড়াচ্ছে ওর শরীরের মধ্য দিয়ে রেহানাকে শক্ত করে ধরে আছে সেজান। ভয়ার্ত চোখে রেহানার দিকে তাকিয়ে আছেন মামী। রেহানার মাথায় পানি ঢালার ব্যবস্থা করেছেন তিনি। আজ খুব খারাপ কিছু ঘটবে মনে হচ্ছে সেজানের। চোখের পানি মুছল সে। খুব কষ্ট হচ্ছে তার।
এভাবেই বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হলো।
সেজানের সব আশঙ্কা ভুল প্রমাণিত করে হঠাৎ তাকাল রেহানা। সেজানের দিকে চেয়ে বলল, ‘পানি খাব।’
সেজান বিস্মিত হলো। দ্রুত এনে দিল পানি। উদ্বিগ্ন গলায় বলল, ‘তোমার এখন কেমন লাগছে?’
‘খুব ভাল লাগছে। কেন জানি মনে হচ্ছে, সুস্থ হয়ে গেছি। পুরো সুস্থ হয়ে গেছি। আচ্ছা, কয়টা বাজে? …তোমার নিশ্চয়ই রাতে খাওয়া হয়নি। ফ্রিজে মাংস আছে। রুটি বানিয়ে দিচ্ছি আমি। আমারও এত খিদে লেগেছে যে, মনে হচ্ছে পঞ্চাশটা রুটি খেতে পারব।’
সেজান বলল, ‘তোমাকে কিছু করতে হবে না। তোমার শরীর অসুস্থ। তুমি ঘুমানোর চেষ্টা করো। কাল ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব তোমাকে।’
হাসিমুখে রেহানা বলল, ‘আমাকে আর ডাক্তার দেখাতে হবে না। আমি সুস্থ হয়ে গেছি।’ আসলেই একদম অন্যরকম লাগছে রেহানার। এতদিন যে ভয়টা বুকে পুষে রেখেছিল, এই মুহূর্তে সেই ভয়টা যেন মুছে গেছে। কেন জানি মনে হচ্ছে, সে আর কোনও দিন দেখবে না সেই ভয়ঙ্কর লোকটাকে।
সেজানের মুখে হাত বুলিয়ে দিল রেহানা। বলল, ‘আমি তোমাকে আমার জীবনের কিছু কথা বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তার আর প্রয়োজন নেই।’
‘প্রয়োজন না থাকলেও বলো।’
‘না। ওই কষ্টের কথাগুলো আমি আর মনে করতে চাই না।’
‘আচ্ছা, তা হলে থাক। বাদ দাও। কষ্টের কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। তবে আমি একটা কথা বলতে চাই তোমাকে।’
‘কী তা?’
‘আমি সব বিপদে তোমার পাশে থাকব। কাপুরুষের মত পালিয়ে যাব না।’
মামী আরেক ঘরে যেতেই রেহানার খুব ইচ্ছা হলো সেজানকে জড়িয়ে ধরতে। কিন্তু লজ্জা-লজ্জা লাগছে। শেষ পর্যন্ত ভালবাসার কাছে লজ্জার পরাজয় ঘটল।
নতুন জীবন শুরু হলো রেহানা ও সেজানের
দশ
আজ নিজের বাড়িতে ফিরে যাচ্ছে আনোয়ার। আবার খারাপ করেছে ওর শরীরটা। সবসময় লেগে থাকছে মাথাব্যথা ও বমি-বমি ভাবটা। খাওয়ার রুচি নেই একদম।
নাদিয়া বলল, ‘আপনার চলে যাওয়াটা কি এতই জরুরি?’
আনোয়ার গায়ের চাদরটা ঠিকমত জড়িয়ে নিল। ‘হ্যাঁ। এখানে থাকতে আর ভাল লাগছে না।’
‘শুনেছেন নিশ্চয়, সুস্থ হয়ে গেছে রেহানা।’
‘হ্যাঁ।’
‘আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, কোনওভাবে রেহানাকে সুস্থ করেছেন আপনি।’
আনোয়ার হাসল। সেই হাসির অর্থ হ্যাঁ বা না-যে-কোনোটাই হতে পারে। নাদিয়া বলল, ‘আমি আপনার অপেক্ষায় থাকব।’
আনোয়ার কিছু বলল না।
আনোয়ারের হাত ধরল নাদিয়া। ঝটকা মেরে হাতটা সরিয়ে দিল আনোয়ার। রাগত স্বরে বলল, ‘কখনও আমার হাত ধরবে না তুমি।’ এরপর পিছনে না তাকিয়ে বাসা থেকে বেরিয়ে গেল ও।
পিছন থেকে এক দৃষ্টিতে ওর চলে যাওয়া দেখল নাদিয়া।
.
চাদর সরিয়ে ওর ডান হাতটা দেখল আনোয়ার। তালুতে বাসা বেঁধেছে কয়েকটা ছোট পোকা। একটা পোকার মুখে ডিমও দেখতে পেল আনোয়ার।
ওর শরীরে ভয়ঙ্কর পোকার বীজ ছড়িয়ে দিয়ে গেছে খান্নাস!
হত্যা
এক
রুখসানাকে মেরে ফেলার পর দুই ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর যখন রুখসানার শরীরটা বিছানায় এলিয়ে পড়ল তখন ঘড়িতে রাত ৮টা বাজে। আর এখন ১০টা। দুই ঘণ্টা একটা লাশকে নিয়ে এক ঘরে থাকাটা বেশ কঠিন একটা বিষয়। তবে ইস্পাত কঠিন স্নায়ুর অধিকারী শওকতের জন্য বিষয়টা তেমন কঠিন নয়। খুনের মত এত বড় বিষয়ও তাকে উত্তেজিত করতে পারেনি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে সে নিশ্চিন্ত মনে সিগারেট টানছে।
রুখসানাকে মেরে ফেলতে শওকতকে তেমন কোনও বেগ পেতে হয়নি। ঘুমের ওষুধ, ছুরি, পিস্তল-এ ধরনের কোনও উপকরণেরই প্রয়োজন পড়েনি। আজ অফিস থেকে ফিরেই রুখসানা খানিকটা সময় মাথা নিচু করে বসে ছিল। তাকে খুব ক্লান্ত লাগছিল। শওকত বুঝতে পেরেছিল কোনও কিছু নিয়ে ঝামেলায় আছে।
রুখসানা বাইরের পোশাক বদলে কড়া গলায় বলে, ‘আমি কিছুক্ষণ ঘুমাব। আমাকে বিরক্ত করবে না।’
কথাটা শুনে খুশি হয় শওকত। বলে, ‘এক গ্লাস শরবত করে দিই? তারপর ঘুমাও।’
‘না। এখন কিছু খাব না। আমাকে প্লিজ বিরক্ত করবে না।’
মুখে একটা দুঃখী ভাব ফুটিয়ে তুলে শওকত বলে, ‘আচ্ছা। ঠিক আছে, তুমি ঘুমাও।’ ঘুমাও কথাটার উপর অত্যাবশ্যক জোর দেয় সে।
রুখসানা ঘুমিয়ে পড়া মাত্রই শওকত আর দেরি করেনি। একটা বালিশ তার মুখের উপর চেপে ধরেছে। ‘বেচারি। বেশ কিছুক্ষণ বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু আমার শক্তির সাথে পেরে ওঠেনি,’ মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ করে নিজেকে বলল শওকত। নিজের সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে তার।
শওকত অবাক হয়ে লক্ষ করল, মারা যাওয়ার পরেও রুখসানার শরীর অনেক গরম। সে শেষবারের মত গভীর মমতায় তার প্রিয় স্ত্রীকে আলিঙ্গন করল তার কপালে চুমু খেল। এরপর তাদের বড় ডিপ ফ্রিজটার মধ্যে রুখসানার লাশট ঢুকিয়ে দিল। অন্য আট-দশটা রাতের মত আজও সে শান্তিতে ঘুমাবে। যদি হঠা দেখে রুখসানা ঘরের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে, তবু খুব বেশি বিচলিত হবে না। ধরে নেবে এসব হ্যালুসিনেশন। ভূতকে ভয় পেলে চলে না। রুখসানার লাশটা কাটাছেঁড়া করার বা কোনও জায়গায় ফেলে দেয়ার কোনও ইচ্ছে নেই। লাশটা ফ্রিজেই থাকবে। আগামীকাল সকালেই বেনাপোল বর্ডার দিয়ে ভারতে চলে যাওয়ার ইচ্ছা তার। কারণ পালিয়ে থাকার জন্য ভারত বেশ উৎকৃষ্ট জায়গা।
প্রিয় বন্ধু আনিসকেও কিছুক্ষণ আগে মেরে ফেলেছে শওকত। তাকে অবশ্য রুখসানার মত সহজে মারতে পারেনি। রিভলভারের দুটো গুলি খরচ করতে হয়েছে। আজ ভুলিয়ে-ভালিয়ে আনিসকে আশুলিয়া নিয়ে যায় শওকত। এরপর একটা জনশূন্য জায়গায় সুযোগ বুঝে…। সে খুব ভাল করেই টের পেয়েছিল আনিসের সঙ্গে রুখসানার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সম্পর্কের উষ্ণতা যে বাড়ছিল সেটাও টের পাওয়া যাচ্ছিল। যে-কোনও সময় হয়তো রুখসানা তাকে ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। এদিকে শওকত অনেক আগেই সব সম্পত্তি স্ত্রীর নামে লিখে দিয়েছে। তাই পাশার দানে হার এড়ানোর জন্য দু’জনকেই হত্যা করতে হলো।
বিছানায় শুয়েই শওকতের কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল। মনে হলো খাটের নীচে কিছু একটা নড়াচড়া করছে। প্রথমে সে বিষয়টা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু মনের ভিতর তীব্র খচখচানি তাকে অস্থির করে ফেলল। অস্থিরতার কাছে পরাজিত হয়ে লাইট জ্বালল শওকত। এরপর খাটের নীচে উঁকি দিল। প্রচণ্ড চিৎকারে চারদিক যেন কেঁপে উঠল। খাটের নীচে আনিস শুয়ে আছে। আনিস শওকতের দিকে এক নজর তাকাল। তারপর নিজের মনে গাইতে লাগল, ‘Where have all the flowers gone?’
দুই
পুরানো দুঃস্বপ্নটা দেখে ঘুম ভাঙল শওকতের। তার হৃৎস্পন্দন হচ্ছে তড়িৎ গতিতে। সঙ্গে যোগ হলো নিঃশ্বাসে কষ্ট। মুখের ভিতরে শুকনো, খটখটে। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তেই এক গ্লাস পানি পান না করলে সে মারা যাবে। শরীরটাও কেমন যেন অবশ হয়ে আসছে। নিজেকে মনে হচ্ছে প্যারালাইসিস রোগী। শওকত বাম হাতটা নাড়ানোর চেষ্টা করল। হ্যাঁ, বাম হাত নাড়াতে পারছে। কিন্তু বাম চোখে ঠিকমত দেখতে পাচ্ছে না। তার পাশে গুটিসুটি মেরে ঘুমাচ্ছে রুখসানা। ও ডাকার চেষ্টা করল, ‘রু-রুখ…’
রুখসানা ঘুমের ভিতরেই অস্ফুট স্বরে ‘উ’ বলল। সুন্দর মায়াবী একটা মুখ, রুখসানার। বিড়ালের মত আদুরে মুখমণ্ডল, ধনুকের মত শরীরের অবয়ব আর কমলার কোয়ার মত কোমল ঠোঁট। আর তার গাঢ় নিঃশ্বাসেও আছে কাছে আসার আহ্বান। স্বল্প পোশাকে তার শরীরের সৌন্দর্য যেন বহুগুণে বেড়ে গেছে। অনাবৃত পা শওকতের শরীরের উপর তুলে দিয়েছে রুখসানা। হালকা আকর্ষণীয় পা-টা শওকতের কাছে এখন ভয়ানক ভারী মনে হচ্ছে।
শওকত আবার বলল, ‘রুখ। অ্যাই, রুখ।
রুখসানা চোখ মেলে তাকাল। আস্তে করে বলল, ‘কী হয়েছে?’
‘ভয় করছে, রুখ। সেই স্বপ্নটা আবার দেখেছি। শরীর খারাপ লাগছে।’
‘কী যে পাগলের মত ভয় পাও। স্বপ্ন তো স্বপ্নই,’ সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বলল সে।
‘আনিস, আনিস আবার এসেছিল।’
‘পানি খাবে?’
‘হ্যাঁ, পানি খাব। পানি।
রুখসানা পানির গ্লাস এগিয়ে দিল।
শওকত এক চুমুক পানি খেয়ে মুখ বিকৃত করল। কাঁপা গলায় বলল, ‘পানি তিতা লাগছে। বমি আসছে।’
রুখসানা কিছুটা বিরক্ত হলো। বেশ কিছুদিন ধরে শওকত এরকম ঝামেলা করছে। লাইট জ্বালল রুখসানা। আলোতেও শরীরের স্বল্প কাপড় নিয়ে বিব্রত হলো না সে।
‘তোমাকে নিয়ে কী যে করি!’ কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রুখসানা। ‘এত কীসের ভয় তোমার?’
‘স্বপ্নে আমি অনেক সাহসী একজন মানুষ। কিন্তু স্বপ্ন ভাঙতেই সব এলোমেলো হয়ে যায়। আজ ঘুমের মাঝে আমি আবার তোমাকে এবং আনিসকে মেরে ফেলেছি।’
‘ওহ। ভাল করেছ। কে জানে হয়তো তোমার হাতেই আমাদের মৃত্যু আছে। হা-হা,’ খিলখিল করে হেসে উঠল রুখসানা।
‘আনিস ভাল আছে তো?’
‘গতকালই না আমাদের বাসায় এল আনিস ভাই।’
‘তবু চিন্তা হচ্ছে। ওর খারাপ কিছু হয়নি তো? স্বপ্নে যা-ই দেখি না কেন, আমি আমার বন্ধুকে অনেক ভালবাসি।’
‘আনিস ভাই মরে গেছে।’ মুখটা বিকৃত করে রুখসানার জবাব।
‘রুখ, দেখো, আমার বুড়ো আঙুলটা কাঁপছে…’
‘শান্ত হও তো।’
‘বিছানার নীচে কেউ আছে কি না একটু দেখবে?’
‘দেখো তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছ!’
‘স্বপ্নে আনিস খাটের নীচে শুয়ে ছিল। আর একটু পরপর শিস বাজানোর চেষ্টা করছিল। আর একটু পর গাওয়ার চেষ্টা করছিল: Where have all the flowers gone. এরপর…’
‘ওহ, বাদ দাও তো এসব। অসহ্য লাগছে,’ বিরক্তিটা পুরোপুরি প্রকাশ করে বলল রুখসানা। ‘তুমি কি আমাকে আর আনিস ভাইকে সন্দেহ করো?’
‘না, না। কখনওই না। আমি জানি তুমি আমাকে কখনওই কষ্ট দিতে পারো না। তবু কেন যে এসব স্বপ্ন দেখি!’
‘তুমি মানসিকভাবে অসুস্থ একজন মানুষ। তোমার চিকিৎসা প্রয়োজন।’
‘তুমি, প্লিজ খাটের নীচটা একটু দেখবে?’
‘ওহ। প্রতিদিন এক ঝামেলা আর ভাল লাগে না। আচ্ছা দেখছি।’
উবু হয়ে খাটের নীচে উঁকি দিল রুখসানা। এরপর একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। একটা আনন্দের ভাব যেন এক নিমিষে পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। মনে হচ্ছে পুরো পৃথিবী যেন স্থির হয়ে গেছে। সত্যিই আনিস খাটের নীচে বসে আছে। চেহারায় জবুথুবু ভাবটা নেই। বরং বড্ড প্রফুল্ল মনে হচ্ছে তাকে। আনিস রুখসানার দিকে না তাকিয়ে গাইতে শুরু করল, ‘How many roads must a man walk down?’
শওকতের চোখ-মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। সে কাঁপা গলায় বলল, ‘রু-রুখ… রুখসানা খেয়াল করল আবারও শওকতের বুড়ো আঙুলটা কাঁপতে শুরু করেছে। রুখসানা উঠে দাঁড়াল। ওয়ারড্রোব খুলল। শওকতের রিভলভারটা খুঁজছে সে। না, নেই। কোথাও নেই সেটা।
আনিস খাটের নীচ থেকে বলল, ‘রু-রুখ।‘
শওকত খাটের উপর থেকে বলল, ‘রু-রুখ।‘
প্রথমজনের কণ্ঠের মধ্যে সন্তুষ্টির ভাব থাকলেও দ্বিতীয়জনের কণ্ঠে ছিল ভয়। রুখসানা পাগলের মত রিভলভারটা খুঁজতে লাগল। হ্যাঁ, রিভলভারটা অবশেষে পাওয়া গেছে। ওটা হাতে নিয়ে পিছনের দিকে ফিরল সে। খাটের নীচ থেকে বেরিয়ে এল আনিস।
শওকত পাগলের মত কাঁপছে। সে বলল, ‘রুখ, আনিস আমাকে মেরে ফেলবে! আমাকে বাঁচাও!’
আনিস বলল, ‘ওহ, বন্ধু। শান্ত হও। এত অস্থির হলে চলে?’
রুখসানা প্রথমে আনিসের দিকে রিভলভারটা তাক করল। এরপর নাটকীয়ভাবে হাতের অবস্থান পরিবর্তন করল। ‘একদম নড়বে না, সোনা। যে স্বপ্নটা তুমি এতদিন দেখে এসেছ সেটা আজ আমরা সত্যি করব,’ শওকতের দিকে তাকিয়ে ঝনঝনে গলায় বলল রুখসানা।
আনিস রুখসানাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, ‘সত্যি করব, তবে একটু অন্যভাবে। আজ তোমাকে মরতে হবে, বন্ধু।’
আনিস সর্বশক্তি দিয়ে শওকতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুখের উপর বালিশ চেপে রাখল। রুখসানাও ওর সঙ্গে যোগ দিল।
আধ ঘণ্টা পরে বাসার বড় ডিপ ফ্রিজে জায়গা করে নিল শওকতের মৃতদেহ। সে রাতেই আনিসকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ে রুখসানা। কাল দেশের বাইরে পালিয়ে যাবে তারা। শওকতের টাকা-পয়সা মোটামুটি সবই ব্যাংক থেকে তুলে নেয়া হয়েছে। নিজের গয়নাগুলোও বিক্রি করেছে রুখসানা। তাই এখন পালিয়ে যেতে পারলেই মুক্তি।
ভোরের দিকে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল আনিসের। প্রচণ্ড ভয় করছে তার। ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন দেখেছে সে। আকুল গলায় সে বলল, ‘রুখ। অ্যাই, রুখ। রুখসানা চোখ মেলে তাকাল। আস্তে করে বলল, ‘কী হয়েছে?’
‘ভয় করছে, রুখ। সেই স্বপ্নটা আবার দেখেছি। শরীর খারাপ লাগছে। ‘কী যে পাগলের মত ভয় পাও। স্বপ্ন তো স্বপ্নই,’ সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বলল সে।
ঠিক তখন ওরা টের পেল খাটের নীচে কিছু একটা খুটখুট আওয়াজ করছে। ফ্যাসফেঁসে গলায় কেউ যেন গান গাওয়ারও চেষ্টা করছে।
আঁধার জগতের খুনি
এক
এক শ’ বিশ বছর পর অন্ধকার জগৎ থেকে মুক্তি পেল ফ্যাফ্যাস নামে দুটি প্রাণী, এখন ঘুরে বেড়াবে তাদের একজন মর্ত্যে। অন্ধকার জগতের জীব ওরা। অসম্ভব বুদ্ধিমান, হিংস্র ও ক্ষমতাশালী। পৃথিবীর দিকে রওনা দেয়ার আগে সঙ্গম করেছে নারী এবং পুরুষ ফ্যাফ্যাস দুটি। এর পরেই মারা গেছে পুরুষটি। নারীটি তার পেটে ডিম নিয়ে চলে এসেছে পৃথিবীতে। বাঁচাতে চাইছে তার সন্তানদের। এখন দরকার পোষক দেহ। মানুষের চেয়ে ভাল পোষক দেহ আর একটিও নেই।
ফ্যাফ্যাসটি প্রথম পা রেখেছে চিনে, কিন্তু জায়গাটা পছন্দ হয়নি তার। যেতে চেয়েছে এই মহাদেশের দক্ষিণে। ওখানকার আবহাওয়া তার সন্তানদের জন্য সেরা। তবে বেশি দেরি করতে পারবে না। ত্রিশ দিনের মধ্যে জোগাড় করতে হবে ভাল পোষক দেহ। একটা কন্টেইনার ভর্তি জাহাজে চেপে বসল ফ্যাফ্যাস, লুকিয়ে থাকল জাহাজের এক নির্জন কোণে। ক্যামোফ্লেজ বিষয়ে খুব পারদর্শী সে। জানে, জাহাজের কেউ তাকে খুঁজে পাবে না। বারোতম দিনে জাহাজটি পৌছাল চট্টগ্রাম বন্দরে। খিদের তাড়নায় এই বারো দিনে জাহাজের তিনজন কর্মীকে কৌশলে মেরে ফেলেছে ফ্যাফ্যাস। মানুষের শরীর ভিটামিনের আধার, ভালভাবে বাঁচতে এই ভিটামিন তার খুব প্রয়োজন।
বাইশতম দিনে জাহাজটি থেকে মাল খালাস শুরু হলে বন্দর থেকে বেরিয়ে পড়ল ফ্যাফ্যাস। আবারও আশ্রয় নিল ক্যামোফ্লেজের। বন্দরের বাইরে অনেক গাড়ি দেখতে পেল সে। এর মধ্যে একটা গাড়ির মালামাল রাখার জায়গায় ঢুকে পড়ল ফ্যাফ্যাস। একটু পর গাড়িটি রওনা দিল রাজধানী ঢাকার দিকে।
গাড়িটি ছিল শিল্পপতি ইলিয়াস মোল্লার।
.
মহাখালি, ঢাকা। রাত একটা।
বার থেকে বাড়ি ফিরছিল জাফর। মদ খেয়ে সহজে মাতাল হয় না সে। তবে আজ তার লিমিট থেকে দুই পেগ বেশি খেয়ে ফেলেছে। ঝিমঝিম করছে মাথাটা। মদ খেয়ে গাড়ি চালাতে গেলে অসুবিধা হবে বলে সে গাড়ি আনেনি। তার বন্ধু ইলিয়াস তাকে উত্তরা তিন নম্বর সেক্টর পর্যন্ত লিফট দিয়েছে। এবার নির্জন দুটো গলি পার হয়ে তাকে বাড়ি যেতে হবে।
গাড়ি থেকে নেমে পড়ল জাফর, টাল সামলে নিয়ে বলল, ‘থ্যাঙ্কস, ইলিয়াস।’
‘সাবধানে যেয়ো, বন্ধু,’ জবাবে বলল তার বন্ধু।
‘রাজার কোনও ক্ষতি হয় না।’
‘দুই পেগ বেশি খেলে সবাই রাজা হয়ে যায়।’
‘হা-হা-হা! ভালই বলেছ, বন্ধু!’
‘বাই।’
গাড়িটা হুশ্ করে চলে গেল। ইলিয়াসের গাড়ি থেকে কিছু একটা বেরিয়ে জাফরের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। জাফরের গান গাইতে ইচ্ছা হচ্ছে। সুজানাকে সে প্রতি রাতে গান শোনায়। সুজানাও তখন গুনগুন করে গান করে। জাফরের মনে হয় অপূর্ব ওর বউয়ের গলা।
সুজানা জাফরের স্ত্রী। দুই বছর আগে তাদের বিয়ে হয়েছে।
সন্তানের মা হতে চলেছে সুজানা। ওদের সন্তানটি মেয়ে।
ওরা মেয়ের নাম ঠিক করে রেখেছে: রোমি।
সপ্তাহে একদিন বার-এ যায় জাফর। সপ্তাহে একদিন ওখানে যাওয়া বোধহয় তেমন দোষের নয়। সুজানারও এ নিয়ে অভিযোগ নেই। আগে প্রায়ই সঙ্গী হত জাফরের। কিন্তু গত দু’মাস ধরে খুব সাবধানে চলতে হচ্ছে তাকে। ভারী হয়ে গেছে শরীর, সামনের মাসেই ডেলিভারি ডেট।
হেলেদুলে হাঁটছে জাফর। খুব নির্জন গলিটা। এ পথ দিয়ে সে প্রায়ই বাসায় ফেরে। কিছুক্ষণ পর তার মনে হলো, কেউ যেন আসছে পিছে-পিছে। সে পিছনে তাকাল, কেউ নেই। ভয়-ভয় করতে লাগল তার। কয়েক মাস আগে গলির মুখে বড় রাস্তায় একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল। মাথা থেঁতলে গিয়েছিল এক বৃদ্ধা মহিলার। কথিত আছে, প্রায় নাকি এখানে দেখা যায় সে মহিলাকে। তিনি নাকি তাঁর থেঁতলানো মাথা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, আর নাকি স্বরে কাঁদতে থাকেন।
আবার সেই খস খস শব্দ। বিকট এক গন্ধ পেল জাফর। গন্ধটায় গুলিয়ে উঠল তার শরীর। রাস্তার পাশে বসে বমি করতে লাগল সে। উঠে দাঁড়াল কিছু সময় পর। দুর্বল লাগছে শরীর। এমন সময় বুঝতে পারল, পিছে দাঁড়িয়ে কেউ 1 পিঠে লাগছে গরম ভাপ। সাহস সঞ্চয় করে পিছনে তাকাল সে। একটা অদ্ভুত, কুৎসিত, ভয়ঙ্কর প্রাণী এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে। প্রাণীটার তিন শুঁড় নড়াচড়া করছে ক্রমাগত। সরীসৃপের মত নমনীয় মাথা, ঘুরে যায় পিছনেও। একটা মাত্ৰ পা, সব মিলে দুটো হাত। প্রয়োজনে হাত ব্যবহার করে পা হিসাবে, বাড়াতে পারে হাঁটার গতি। হাত-পায়ে ধারাল নখ। সূচালো দাঁত ঢেকে রাখার জন্য ঠোঁট নেই। বিশাল নাক দিয়ে শুঁকে দেখছে সে জাফরকে।
হ্যাঁ, তার পছন্দ হয়েছে জাফরকে। দেরি করল না প্রাণীটা। শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে ধরল জাফরকে। সূচালো দাঁত বসিয়ে দিল ওর গলায়। চিৎকার করারও সুযোগ পেল না জাফর।
কাজ শুরু করে দিয়েছে প্রাণীটা। নখ দিয়ে ছিঁড়ে ফেলল জাফরের বুক থেকে পেট পর্যন্ত। ওখানে হাত ঢুকিয়ে তৈরি করল গর্ত। জাফরের দেহে ঢুকে গেল নিজে। আর তখনই জাফরের শরীরের গর্তটা মিলিয়ে গেল। কিন্তু শরীরে রয়ে গেল কাটা দাগের চিহ্ন।
এখন থেকে জাফরের শরীর ব্যবহার করবে ফ্যাফ্যাস, নিয়ন্ত্রণ করবে শারীরবৃত্তীয় সব কাজ। অর্ধমৃত জাফর এখন অন্ধকার জগতের ভয়ঙ্কর প্রাণী ছাড়া কিছুই নয়।
তার শরীরে ডিম দেবে ফ্যাফ্যাস। দু’ সপ্তাহে জাফরের শরীরের যেন কোনও ক্ষতি না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখবে। দুই সপ্তাহ এই পোষক দেহে থাকতে হবে তাকে। এ সময়ে জাফরের বড় কোনও ক্ষতি হলে, সে-ও বাঁচবে না।
দু’ সপ্তাহ পর যখন ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোবে, এমনিতেই মারা যাবে জাফর। মরবে ভয়ঙ্কর ফ্যাফ্যাসও। কিন্তু থেকে যাবে তার অসংখ্য বাচ্চা এই পৃথিবীতে।
তাদের থেকে জন্ম নেবে আরও বাচ্চা। এক সময় পৃথিবী হবে ফ্যাফ্যাসদের রাজ্য, শাসন করবে তারা গোটা এই জগৎ।
দুই
কাল রাতের ঘটনায় প্রচণ্ড অবাক হয়েছে সুজানা। রাতে কখন জাফর বাসায় ফিরেছে, সে কিছুই টের পায়নি। জাফর অন্য একটা রুমে দরজা বন্ধ করে ঘুমাচ্ছে। এমন তো কখনও করে না!
সুজানা দরজা ধাক্কাতে ধাক্কাতে বলল, ‘জাফর, অ্যাই, জাফর!’
জাফর উঠে দরজা খুলল, চোখ-মুখ অন্যরকম। তাকিয়ে থাকলে কেমন যেন
আতঙ্ক লাগে। সুজানা বলল, ‘কী হয়েছে, জাফর, তোমার?’
জাফর কিছু না বলে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।
জাফরের হাত ধরে কেঁপে উঠল সুজানা।
জাফরের হাতটা বরফের মত ঠাণ্ডা। ‘জ-জ-জাফর!’
এবার হাত বাড়িয়ে দিল জাফর। বড় হতে লাগল ওর নখগুলো। বিচিত্র ভাষায় কিছু বলতে লাগল জাফর। প্রাচীন গ্রীক ভাষা? সুজানাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল জাফর।
মেঝেতে ছিটকে পড়ে গেছে সুজানা, ঠোঁট কেটে গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোঁটা রক্ত।
‘কে তুমি?’ সুজানার গলায় শঙ্কা এবং আতঙ্ক।
‘থাকব, আমি থাকব,’ গলায় শ্লেষ নিয়ে বলল জাফর। বেশ বোঝা গেল তার হিংস্রতা। বাংলা কথাগুলো তেমন গুছিয়ে বলতে পারছে না। তবে কথাগুলোর মূল ইঙ্গিতটা বুঝতে সমস্যা হলো না।
সুজানা কাঁপা গলায় জানতে চাইল, ‘তোমার কী হয়েছে, জাফর?’
কিন্তু জাফরের উত্তর একই: সে থাকবে। তাকে থাকতেই হবে।
ইঙ্গিতটা পরিষ্কার, সুজানা তাকে না ঘাঁটালে সে-ও ঘাঁটাবে না সুজানাকে।
সুজানা বুঝল, অশুভ কিছু ভর করেছে জাফরের উপর। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে থাকল, কী করবে।
ঠিক করল, ওখান থেকে সরে এসে মাকে ফোনে সব খুলে বলবে। কিন্তু মোবাইল ফোন কানে তুলে বুঝল সিগনাল নেই। জাফরের শরীর থেকে বেরোচ্ছে নীল রঙের আভা। সুজানার কেন জানি মনে হচ্ছে, জাফরের কারণেই এই ঘরে মোবাইল নেটওঅর্ক কাজ করছে না। বাসা থেকে বেরোনোর চেষ্টা করল সুজানা। কিন্তু জাফর পথ আগলে দাঁড়াল। মাথা নাড়িয়ে বুঝিয়ে দিল ও বের হতে পারবে না।
দু’ সপ্তাহের জন্য ফ্যাফ্যাসের কাছে বন্দি সুজানা। কোনও ভুল বা চালাকি করলে ওকে মেরে ফেলবে ফ্যাফ্যাস।
জাফর ইঙ্গিতে বোঝাল, সে ক্ষুধার্ত। নিজের পেট এবং সুজানার পেটের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, ‘তোমার পেটে বাচ্চা। আমার পেটে বাচ্চা বেঁচে থাকবে। অবশ্যই বেঁচে থাকবে। আমার বাচ্চা মারা গেলে তোমার বাচ্চাও মারা যাবে।’
মাথা কাজ করছে না সুজানার। আতঙ্কে ওর শরীর ভারী হয়ে আসছে। চোখের সামনে সবকিছু কেমন যেন ঝাপসা।
সুজানা বলল, ‘কী খেতে চাও?’
একটু হাসল জাফর। বলল, ‘মানুষ চাই। মানুষ নিয়ে আসো।
‘কী? মানুষ!’
‘হ্যাঁ। ডেকে আনো। ওটা দিয়ে ডেকে আনো।’ মোবাইলের দিকে আঙুল তুলে দেখাল জাফর।
‘কাকে ডেকে আনব? এসব কী বলছ?’
মুহূর্তেই রক্ত হিম হয়ে গেল জাফরের চোখ। স্পষ্ট বোঝা গেল রাগ। ফুঁসে উঠে জাফর বলল, ‘ডেকে আনো। ডেকে আনো। না হলে তোমাকে…’
এবার জাফর বুঝিয়ে দিল কাউকে ফোন করে ডেকে না আনলে, সে ক্ষুধা মেটাবে সুজানাকে দিয়েই। সুজানার মোবাইলের নেটওঅর্ক ফিরে এসেছে। বুঝে উঠতে পারল না, কাকে ফোন দেবে সে? কাকে মেরে ফেলার জন্য আমন্ত্রণ জানাবে? কিন্তু ও জানে, জাফরের কথা না শুনলে মারা পড়বে।
সুজানা তার বান্ধবী সুমিকে ফোন দিল। চোখের পানি বাঁধ মানতে চাইছে না। তবু গলা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে ও বলল, ‘হ্যালো, সুমি।’
‘হ্যালো, সুজ। কী খবর তোর?’
‘ভাল। আমার বাসায় একটু আসতে পারবি? খুব দরকার।’
‘অবশ্যই। জাফর ভাইয়া বাসায় নেই?’
‘আছে। তোকে খুব মনে পড়ছে।’
‘আচ্ছা, আমি এক ঘণ্টার মধ্যে আসছি। রিমিকেও নিয়ে আসছি।’
‘রিমিকে না আনলে হয় না?’
‘আমার বাসায় কেউ নেই রে। বাচ্চা মেয়ে একা-একা কী করে থাকবে?’
‘আচ্ছা, নিয়ে আয় তা হলে।’
‘ওকে।’
‘আর একটা কথা, আমার বাসায় আসার কথা কাউকে বলার দরকার নেই।’
‘মানে?’
‘একটু ব্যক্তিগত ব্যাপারে তোর সাথে কথা বলব। তাই আমার বাসায় আসার ব্যাপারটা কাউকে বলিস না। দুলাভাইকেও না।’
‘আচ্ছা, ঠিক আছে। আমি আসছি। তুই ঠিক আছিস তো, সুজ?’
‘হ্যাঁ। ঠিক আছি।’
মোবাইলের লাইন কেটে গেল। সুজানার খুব ঘুম আসছে। জাফরের শরীর থেকে হঠাৎ এক ধরনের গ্যাস বেরোচ্ছে। সেই গ্যাসের প্রভাবে কেমন শরীর এলিয়ে আসছে সুজানার। চোখের পাতা ভারী হয়ে এল। সুজানা ঘুমিয়ে পড়ার পর ওর দেহটা কাঁধে তুলে নিল জাফর। বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দিল ওকে।
জাফর অপেক্ষা করছে শিকারের জন্য।
.
এক ঘণ্টার মাঝেই সুজানার বাসায় পৌছে গেল সুমি আর তার মেয়ে রিমি। একবার ডোরবেল বাজতেই দরজা খুলে দিল জাফর। ওকে দেখে সপ্রতিভ হাসি হেসে সুজানা বলল, ‘জাফর ভাই, কেমন আছেন? সুজানা হঠাৎ জরুরি তলব করল। তাই চলে এলাম।’
জাফর কিছু বলল না। শুধু নাক দিয়ে ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করল। ‘কী, আপনি কিছু বলছেন না যে? সুজানার সাথে ঝগড়া হয়েছে নাকি?’ জিজ্ঞেস করল সুমি।
জাফর এবারও জবাব দিল না। ওর দিকে তাকিয়ে অবাক হলো সুমি। বরফের মত শীতল চোখ। যেন তীব্রভাবে ফুটে উঠেছে কপালের রগ। গা থেকে আসছে কেমন একটা বাজে গন্ধ।
সুমিকে তার পিছন-পিছন আসতে ইঙ্গিত করল জাফর।
সুমি এগিয়ে গেল।
রিমি অবশ্য মায়ের দিকে লক্ষ করছে না, মন দিয়ে টিভিতে কার্টুন দেখছে।
সুমিকে পাশের রুমে নিয়ে গেল জাফর। পিছনে বন্ধ করল ঘরের দরজাটা।
একটু চমকে উঠে বলল সুমি, ‘দরজা বন্ধ করছেন কেন, জাফর ভাই?’
হাসল জাফর। সে হাসি ভয়ঙ্কর।
সুমি কিছু বোঝার আগে ওর বুক চিরে হাতটা ঢুকিয়ে দিল জাফর। এক ঝটকায় বের করে আনল হৃৎপিণ্ডটা।
সুমি এক সেকেণ্ড চেয়ে রইল জাফরের দিকে, তারপর ঢলে পড়ে গেল মেঝেতে। রক্ত ভর্তি হৃৎপিণ্ড কামড়ে খেতে শুরু করেছে জাফর। আহ্, কী স্বাদ! আনন্দে বুজে এল তার চোখ। খাওয়া শেষ করে সুমির পোশাক ছিঁড়ে ফেলল জাফর। দেহের নরম অংশগুলো খেতে শুরু করেছে। এক ঘণ্টার মধ্যে সুমির শরীরের অর্ধেকটা খেয়ে ফেলল জাফর। হাড়গুলো অবশ্য খেল না। হাড় তার পছন্দ নয়। খাওয়া শেষে তৃপ্তির ঢেকুর তুলল। এমন সময় রুমের দরজা ধাক্কাতে লাগল রিমি।
‘মামণি, মামণি? কোথায় তুমি?’
বেড়ে গেল জাফরের চোখের উজ্জ্বলতা। আরও একটা শিকার। ছোট বাচ্চার দেহ। অনেক বেশি মজার। রুমের দরজাটা খুলে দিল জাফর। ওর শরীরে রক্ত দেখে চিৎকার করে উঠল রিমি। কিন্তু ওর মাথাটা সর্বশক্তি দিয়ে নিজের দিকে টেনে নিল জাফর। চার বছরের বাচ্চা এত প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করতে পারল না। শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল মাথাটা। কিন্তু তখনও কয়েক সেকেণ্ড নানাদিকে তাকাল রিমির চোখ। মাকে খুঁজছিল বেচারি।
এখন কিছুক্ষণ ঘুমাবে জাফর। সাড়ে পাঁচ ঘণ্টার টানা ঘুম। আগেই সুজানাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে সে। তার ঘুম ভাঙতে কমপক্ষে সাত ঘণ্টা লাগবে।
তাই পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমাতে গেল জাফর।
তিন
সাত ঘণ্টা পর…
ঘোরটা আস্তে-আস্তে কেটে যেতে থাকল সুজানার। কেমন যেন দুর্বল লাগছে শরীর, ঘুরছে মাথাটাও। চারদিকে যেন উড়ছে ধোঁয়া। চোখ মেলে তাকাল সে। দেখল জাফরের ভয়ঙ্কর মুখ। তার শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জমাট রক্ত।
ঠিক সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা পর ঘুম ভেঙেছে জাফরের। ঘুম ভাঙার পর থেকে সুজানার ঘুমন্ত শরীরের পাশে বসে আছে। তার বারবার মনে হয়েছে, সুজানাকে মেরে ফেলবে, নাকি বাঁচিয়ে রাখবে। শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখার সিদ্ধান্তই নিয়েছে। কারণ সুজানা তাকে আরও শিকার ধরতে সাহায্য করতে পারবে। জাফরের শরীর নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না ফ্যাফ্যাস। নিজে শিকার ধরতে গেলে যে- কোনও আঘাতে ক্ষতি হতে পারে জাফরের শরীরের। আর তার মানেই সন্তানের ক্ষতি। সেটা সে হতে দেবে না।
জাফরকে দেখে লাফিয়ে উঠে বসল সুজানা। ওড়নাটা ভাল করে জড়িয়ে নিল গায়ে। জাফরের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘কী-কী-কী…চাই?’
‘তরল খাবার খাব। পুষ্টিকর তরল। চাই। অনেক চাই।’
‘কী পুষ্টিকর তরল?’
‘রাত হয়েছে। পুষ্টিকর তরল চাই। রাতে পুষ্টিকর তরল খাব।’
‘পানি চাও?’
‘নাহ্!’ রেগে উত্তর দিল জাফর।
‘তা হলে দুধ?’
‘হ্যাঁ, দুধ। দুধ চাই। চারপেয়ে জন্তুর।’
ফ্রিজ থেকে দুধের পাতিল বের করল সুজানা। এক লিটার দুধ আছে সেখানে। পিছন-পিছন এসেছে জাফরও। সুজানার হাত থেকে ছিনিয়ে নিল পাতিলটা। ঢক-ঢক করে পুরোটা দুধ খেয়ে ফেলল। এক লিটার দুধ খেতে তার লাগল চার মিনিট। ডিমের ভিতর থাকা তার সন্তানের চাই প্রচুর পুষ্টি। তাদের দিতে হবে উপযুক্ত খাবার, নইলে দুর্বল রয়ে যাবে।
একটা ঢেকুর তুলল জাফর। হঠাৎ বিশ্রী গন্ধে ভরে গেল ঘরটা। সুজানা ভাবছে, সুমি কি এসেছিল? জাফরের সারা শরীরে এই রক্ত কার? সুমির নয়তো? ভয়ের শিহরণ বয়ে গেল ওর সারা শরীরে। জাফর যে রুমে সুমি-রিমিকে মেরেছে, সেই রুমে ঢুকল সুজানা। আর্তচিৎকার দিয়ে উঠল ভয়ে। সুমি আর রিমির শরীরের অংশবিশেষ এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কোথাও হাড়, কোথাও ফুসফুস, কোথাও কিছু মাংস। ওগুলো ঘিরে ধরেছে রাজ্যের পিঁপড়া।
জাফরের আর ওই বাকি খাবারের প্রতি আগ্রহ নেই। কাল সকালে চাই তার নতুন খাবার। আর প্রতি রাতে চাই পুষ্টিকর তরল: দুধ।
সুজানার চিৎকার শুনে দৌড়ে এসেছে জাফর, চেপে ধরল সুজানার গলা। হিসহিসে গলায় বলল, ‘মেরে ফেলব! একদম মেরে ফেলব!’
মুহূর্তেই চুপ হয়ে গেল সুজানা। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিতভাবে কাঁপতে থাকল তার শরীর। সুজানাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল জাফর।
সোফায় গিয়ে বসে পড়ল সুজানা। আর শক্তি নেই দাঁড়াবার। বারবার সুজানার মনে হতে থাকল, এটা কি কোনও দুঃস্বপ্ন? ঘুম ভেঙে সে কি দেখবে তার পাশে ঘুমিয়ে আছে জাফর?
কিন্তু সুজানা বুঝতে পারছে, এটা আসলে মোটেও দুঃস্বপ্ন নয়। তার থেকেও অনেক বেশি কিছু। সে-রাতটা না ঘুমিয়ে কাটাল জাফররূপী ফ্যাফ্যাস আর সুজানা।
সুজানা বুঝল, যে-কোনও জিনিস খুব দ্রুত শিখতে পারে প্রাণীটা। ও জানতে চাইল, ‘কী চাও তুমি?’
‘আমি আমার সন্তানের জন্ম দিতে চাই।’
‘জাফরকে ছেড়ে দাও।’
‘না। না। এই শরীর এখন আমার। আমার সন্তানরা এখানেই জন্ম নেবে। এই শরীরের কোনও ক্ষতি হতে দেব না।’
‘তা হলে আমাকে ছেড়ে দাও। আমিও আমার সন্তানকে বাঁচাতে চাই। আমাকে মেরে ফেলো না।’
হেসে উঠল জাফর। বলল, ‘আমার বাচ্চা জন্ম নেয়ার পর তোমাকে ছাড়ব। এই কয়েকদিন আমার খাবার চাই। শিকার চাই। তুমি শিকার এনে আমাকে দেবে। তোমাকে আমি মারব না।’
‘আমি পারব না। আমি আর কাউকে আনতে পারব না।’
‘তা হলে তুমি আর তোমার সন্তান আমার খাবার আর পিপাসা মেটাবে।’
‘না-না! এমন কোরো না, আমার সন্তানকে বাঁচতে দাও।’
‘আমার সন্তানকে বাঁচতে দিলে আমিও তোমার সন্তানকে বাঁচতে দেব।’
‘তুমি কে?’
‘ফ্যাফ্যাস।’
‘তুমি কোথা থেকে এসেছ?’
‘অন্ধকার জগৎ থেকে।’
‘কে তোমাকে পাঠিয়েছে?’
‘অন্ধকারের দেবতা।’
‘তোমার সন্তানদের কেন এই পৃথিবীতে রাখতে চাও?’
‘আমার সন্তানরা পৃথিবীতে রাজত্ব করবে। চোদ্দ দিন পর পৃথিবীটা হবে ফ্যাফ্যাসের।’
আঁতকে উঠল সুজানা। কী বলছে ফ্যাফ্যাস। এই ভয়ঙ্কর প্রাণীটা ধীরে-ধীরে ধ্বংস করে দেবে পৃথিবীকে? এখন কী করবে ও?
চার
সারাটা রাত এই ভয়ঙ্কর প্রাণীটার সাথে থেকে বুকের ভিতরে কেমন যেন হাঁসফাঁস করতে থাকল সুজানার। মনে হলো, মৃত্যু তার খুব কাছে। সবচেয়ে প্রিয় মানুষটা ঘরেই আছে, কিন্তু সেই প্রিয় মানুষটার মাধ্যমে আজ বিপদের মুখে গোটা পৃথিবী। নিজ রুমে শুয়ে আছে সুজানা। মোবাইল নেটওঅর্ক এখনও কাজ করছে না। সুজানার রুমে বসে আছে জাফরও। একা রাখবে না সে সুজানাকে, কারণ সুজানা যে-কোনও সময় চাতুরির আশ্রয় নিতে পারে। জাফর সেটা হতে দেবে না।
সকাল দশটায় বেজে উঠল বাড়ির ডোরবেল। এতক্ষণ ঝিমুনির মধ্যে ছিল জাফর। হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। সুজানাকে বলল, ‘দেখো, কে এসেছে? কিন্তু কোনও ভুল করলে…’
সুজানা ভয়ে-ভয়ে মাথা নাড়ল। সদর দরজা খুলে দেখল দুধওয়ালা ছেলেটা এসেছে।
সুজানা তার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ইয়ে, মানে, করিম, আজ দুই লিটার দুধ দিতে পারবে?’
‘জী, আপা, পারব।’
‘আচ্ছা, দাও তা হলে।’
‘আজ কোনও অনুষ্ঠান নাকি, আপা? বিশেষ কিছু রান্না করবেন?’
কিছু না বলে ঢোক গিলল সুজানা। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে জাফররূপী ফ্যাফ্যাস। স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে সুজানার দিকে।
সুজানা কোনও চালাকি করলে মেরে ফেলবে।
সুজানার বারবার মনে হচ্ছে, করিমকে কোনও ইঙ্গিত দেবে কি না। একবার যদি কাউকে বিষয়টা বলা যেত, তো ফ্যাফ্যাস এত সহজে পার পেত না। করিমকে ঘরে ঢোকানোও বিপজ্জনক হবে। হয়তো আরও একটা প্রাণ নেবে ফ্যাফ্যাস।
করিম হঠাৎ মুখ বিকৃত করে বলল, ‘আপা, আপনার ঘরের ভিতর থেকে কেমন পচা গন্ধ আসছে।’
রক্তশূন্য হয়ে গেল সুজানার চোখ-মুখ। পচতে শুরু করেছে সুমি আর রিমির দেহের অবশিষ্ট।
করিমকে বিদায় করতে চোখ গরম করে সুজানাকে ইঙ্গিত করল জাফর।
সুজানা বলল, ‘মনে হয় কোথাও ইঁদুর মরে পড়ে আছে।’
‘কী বলেন, আপা, আপনাদের বাসায় ইঁদুর! গন্ধটা কেমন যেন অন্যরকম ইঁদুর মরা গন্ধ নয়। কেমন যেন…’
কথা শেষ না করে মাথা চুলকাতে থাকল করিম
করিমকে ‘তুমি এবার এসো,’ বলে বিদায় করে দিল সুজানা। ফ্রিজে রেখে দিল দুই লিটার দুধ।
করিম চলে যেতেই পুরো ঘর ফিনাইল দিয়ে মোছার চেষ্টা করল সুজানা। তাতে এতটুকু কমল না ঘরের গন্ধ। দুপুরের দিকে অল্প কিছু শুকনো খাবার খেয়ে নিল সুজানা। এই অসীম বিপদেও না খেয়ে থাকতে পারে না মানুষ। মৃত্যু খুব কাছে থাকলেও তাকে খেতে হবে। তার নিজের সন্তানের জন্যও তাকে খেতে হচ্ছে। সুজানাকে খেতে দেখে ফ্যাফ্যাসেরও খিদে লাগল বোধহয়। সে সুজানার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘খিদে! আবার শিকার চাই!’
‘না, না, আমি এসব পারব না,’ ভাঙা গলায় বলল সুজানা।
প্রচণ্ড জোরে সুজানাকে ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ফেলে দিল জাফর।
আছড়ে পড়ে কয়েক মুহূর্ত চোখে-মুখে অন্ধকার দেখল সুজানা। জাফর হিংস্র গলায় আবার বলল, ‘আমার কথা না শুনলে তোকে এবং তোর সন্তানকে মেরে ফেলব আমি। আমার খিদে লেগেছে। শিকার চাই। ফোন কর।’
মোবাইলে নাম্বারগুলো দেখতে থাকল সুজানা। তার মধ্যে ভয়ের এবং বিষাদের অনুভূতি মিলেমিশে একাকার। বারবার চোখের পানি মুছতে হচ্ছে তাকে। দুই-তিনজন বান্ধবীকে ফোন দিল সুজানা। কিন্তু তারা সবাই ব্যস্ত, তাই সুজানার বাসায় আসতে রাজি হলো না। অনেক চিন্তা-ভাবনা করে সে ফোন দিল জামিল ভাইকে। জামিল ভাইয়ের সব সময়ই সুজানার প্রতি একটা দুর্বলতা ছিল। কিন্তু সুজানা সেই দুর্বলতা একদম পাত্তা দেয়নি বলে ব্যাপারটা বেশি দূর এগোয়নি। সুজানার বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর জামিল কমিয়ে দেয় সুজানার সাথে যোগাযোগ। কারণ সুজানার জীবনে সে উপদ্রব হতে চায়নি।
সুজানার ফোন পেয়ে সত্যিই খুব অবাক হলো জামিল। ‘সুজানা? কেমন আছ?’
‘ভাল আছি, জামিল ভাই। আপনি কেমন আছেন?’
‘ভালই আছি।’
‘আপনার সাথে একটু দরকার ছিল। আমার বাসায় একটু আসতে পারবেন?’
‘এখন? এই দুপুরে?’
‘হ্যাঁ। আপনি তো হাউস বিল্ডিং-এ থাকেন। তিন নম্বর সেক্টর পর্যন্ত আসতে খুব বেশি সময় লাগবে না। নাকি অন্য কোনও কাজে ব্যস্ত?’
‘না, মানে, ব্যস্ত না। তোমার বাসায় তো আগে কখনও যাইনি।’
‘বাসা চেনেন তো?’
‘হ্যাঁ। বাসা চিনি। খুব ভালভাবেই চিনি। আচ্ছা, তোমাদের গেটে কি দারোয়ান আছে?’
‘না। কোনও দারোয়ান নেই। আপনি দ্রুত চলে আসুন।’
‘আচ্ছা। আমি কিছুক্ষণের মধ্যে আসছি।’
সুজানার কোনও অনুরোধ ফেলা জামিলের পক্ষে সম্ভব নয়। সে আসলে জরুরি একটা কাজে বেরোচ্ছিল, কিন্তু এখন তার সবচেয়ে জরুরি কাজ সুজানার সাথে দেখা করা।
.
বেজে উঠল ডোরবেল।
দরজা খুলে দিল সুজানা, জামিলের সঙ্গে দু’চার কথা বলবার পর ড্রয়িং রুমে বসাল মানুষটাকে।
সুজানা অস্বস্তির হাসি হাসছে। ও যে প্রেগন্যান্ট, তা জানত না জামিল। এসব নিয়ে কথা বলবে ভাবছে, এমন সময় হঠাৎ পচা একটা গন্ধ নাকে এল ওর। ঘরের ভিতরটা লাগছে বেশ ধোঁয়া-ধোঁয়া। চাপা গলায় আওয়াজ করছে কেউ যেন। কেন জানি বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল জামিলের। কেউ যেন তাকে বলছে, তুমি চলে যাও। এখান থেকে চলে যাও। নিজের মধ্যে তৈরি হওয়া খারাপ অনুভূতিটা পাত্তা দিল না সে। সুজানার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘কী কারণে ডাকলে আমাকে, সুজানা?’
আশপাশে তাকাল সুজানা। দেখতে পেল না জাফরকে। দ্রুত ফিসফিস করে বলে উঠল সুজানা, ‘জামিল ভাই, আমার খুব বিপদ। জাফরের উপরে ভর করেছে এক ভয়ঙ্কর প্রাণী। ও সবাইকে মেরে…’
কথা শেষ করতে পারল না সুজানা।
এসে পড়েছে জাফর। ওকে দেখে উঠে দাঁড়াল জামিল।
‘ভাল আছেন, জাফর ভাই? আমাকে চিনেছেন? আমি জামিল। আপনাদের বিয়ের দিনে পরিচয় হয়েছিল।’
জাফর নাক দিয়ে শব্দ করছে। খুব কাছে এসে শুঁকে দেখল জামিলকে। এর শরীরটা খুব বেশি পছন্দ হয়নি তার। তবু এটা দিয়েই এখন ভরাবে পেট। হঠাৎ জামিলের গলা চেপে ধরল জাফর।
ছটফট করতে শুরু করেছে জামিল। একটু অক্সিজেনের জন্য আঁকুপাঁকু করছে। দুই হাতে হামলা ঠেকাতে চাইল। কিন্তু ভাবলেশহীনভাবে জামিলের দিকে তাকিয়ে রইল জাফর। এতটুকু আলগা হলো না বজ্রমুষ্টি। কিছুক্ষণের মধ্যে মারা গেল জামিল। দূরে চোখ বন্ধ করে সোফাতে বসে থাকল সুজানা। কিছু দেখতে চাইছে না। কিছুই না।
জামিলের চুল ধরে টেনে পাশের ঘরটায় নিয়ে গেল জাফর। এই ঘরেই মেরেছিল সে সুমি আর রিমিকে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে খণ্ড-বিখণ্ড করল জামিলের লাশটা। পুরো বুক, পেট লম্বালম্বিভাবে চিরে ফেলে খেতে শুরু করল। চোখ দুটো তুলে মুখে দিল প্রথমে। এরপর ঊরুর মাংস, পেটের ভিতরের চর্বি খেল। ঘরে রক্তের গন্ধ তীব্র থেকে তীব্রতর হলো।
বাইরে বেসিনে বিকট শব্দে বমি করতে থাকল সুজানা।
1
খাওয়ার মাঝপথে উঠে এল জাফর। সুজানাকে আবার ঘুম পাড়িয়ে দিল তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আবার খাওয়া শুরু করল। খাওয়ার আনন্দে যেন অবশ হয়ে আসছে তার পুরো শরীর।
পাঁচ
ঘুম ভাঙতে শুরু করেছে সুজানার। চোখ মেলে গতকালের মত আজও দেখতে পেল জাফরকে। ধড়মড় করে উঠে বসল সে। জাফর তার দিকে তাকিয়ে ক্রূর হাসি হাসল। বলল, ‘তুমি কী খেতে চাও?’
‘কী?’
‘মানুষের রক্ত, মাংস, চোখ, চর্বি?’
‘না! না! না!’ শরীরের ভিতরটা গুলিয়ে উঠেছে সুজানার।
‘আমি তোমার জন্য রেখেছি। খাও। অনেক পুষ্টি। পুষ্টি প্রয়োজন তোমার সন্তানের।’ হেসে উঠল জাফর।
সুজানার সাথে মজা করছে সে।
সুজানা অবাক হয়ে লক্ষ করল, এই প্রথম তার মধ্যে তীব্র ভয়ের অনুভূতিটা কাজ করছে না। সে জাফরের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট গলায় বলল, ‘আমার সাথে মজা করবে না।’
কঠিন হয়ে গেল জাফরের চোখ-মুখ। সে বলল, ‘রাত হয়ে গেছে। আমার এখন পুষ্টিকর তরল, দুধ প্রয়োজন। দুধ নিয়ে এসো আমার জন্য।’
‘দুধ কি গরম করে আনব?’
‘আনো।’
জাফর ড্রয়িং রুমে গা এলিয়ে বসে আছে। রান্নাঘরে ঢুকে দুধ গরম করছে সুজানা। তার পুরো শরীর কাঁপছে উত্তেজনায়। কারণ পঁচিশটা ঘুমের ওষুধ দিয়েছে সে দুধের মধ্যে। ওই ক’টা ওষুধই ছিল তার কাছে। রাতে ঠিকমত ঘুম না হওয়ায় তাকে প্রতি রাতে একটা করে ওষুধ খেতে বলেছিল ডাক্তার। সেই ওষুধগুলোই কাজে লাগাতে চাইছে। কিন্তু তার পরিকল্পনা কি কাজে আসবে? জাফর কি ঘুমিয়ে পড়বে?
নিজেকে খুব স্বাভাবিক রেখে পাতিল ভর্তি দুধ জাফরের সামনে রাখল সুজানা। জাফর একটু অন্য দৃষ্টিতে তাকাল সুজানার দিকে। তারপর তাকাল পাতিলের দুধের দিকে। ধক ধক করছে সুজানার বুক। মনে হচ্ছে, বুকের ভিতরের শব্দটা বাইরে থেকে শোনা যাবে। কোনও কিছু কি আন্দাজ করছে জাফর? আটকে থাকা নিঃশ্বাসটা বের হয়ে এল সুজানার। দুধ খাওয়া শুরু করেছে জাফর। সুজানা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে। সাত মিনিটের মধ্যে দেড় লিটার দুধ শেষ করল জাফর। বাকিটুকু আর খেতে চাইল না।
সুজানার দৃষ্টি এখনও জাফরের উপর নিবদ্ধ। দেখে মনে হচ্ছে পড়ছে না তার চোখের পলক।
হঠাৎ বলল জাফর, ‘ঝিমঝিম। ঝিমঝিম।’
সুজানা গলা যথাসম্ভব স্বাভাবিক রেখে বলল, ‘কী ঝিমঝিম?’ চেষ্টা করা সত্ত্বেও তার গলায় উত্তেজনার ছাপ ফুটে উঠেছে।
‘মাথা ঝিমঝিম। খারাপ। খারাপ লাগে আমার।’ দশ মিনিট ধরে কেমন যেন এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়াল জাফর। এরপর দড়াম করে পড়ে গেল মেঝেতে।
দ্রুত রান্নাঘর থেকে চাপাতিটা নিয়ে এল সুজানা। গত বছর কুরবানির ঈদে কিনেছিল ওটা।
জাফরের চোখ বন্ধ। কেমন যেন থেমে আছে নিঃশ্বাস।
দেরি করল না সুজানা। সবটুকু রাগ, সবটুকু ক্রোধ জাফরের শরীরে ঢালতে শুরু করল। প্রথমে চাপাতি দিয়ে কেটে দিল জাফরের গলাটা। রক্তে মাখামাখি হয়ে গেল সুজানার গা। জাফরের হাত ও পায়ের রগগুলো কেটে দিল। তারপর এলোপাথাড়ি কোপ দিতে শুরু করল শরীরে। সুজানার পুরো শরীরে ক্রোধের আগুন জ্বলছে। ভয় নেই, আতঙ্ক নেই, আছে শুধু ক্রোধ।
ঠিক এই সময় চোখ খুলে গেল জাফরের। ঘুমের ওষুধের প্রভাব মাত্র পনেরো মিনিট কাজ করেছে ফ্যাফ্যাসের উপর। কিন্তু এই পনেরো মিনিটেই অনেক বড় সর্বনাশ করে দিয়েছে সুজানা ফ্যাফ্যাসের। রক্তে ভেসে যাচ্ছে জাফরের পুরো শরীর। ওঠার চেষ্টা করেও পড়ে গেল সে। ফ্যাফ্যাসের পোষক দেহটা মারা যাচ্ছে। তীব্র এক আর্তনাদ করে উঠল ফ্যাফ্যাস। সেই আর্তনাদের শব্দ অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। জাফরের শরীর থেকে বেরিয়ে পড়ল ফ্যাফ্যাস। কিছুক্ষণ কাঁপতে থাকল জাফরের দেহটা, তারপর হয়ে গেল পুরোপুরি নিশ্চল। ফ্যাফ্যাস বুঝতে পেরেছে, তার আয়ু শেষের দিকে।
ফ্যাফ্যাসের আসল চেহারা দেখতে পেল সুজানা। ভয়ঙ্কর এই চেহারা দেখে যেন নড়ে উঠল সুজানার পেটের সন্তানও। সুজানার মনে হলো, তার সন্তান পেটের মধ্য থেকে বলছে, ‘মা, আমাকে বাঁচাও!’
নীচে পড়ে থাকা চাপাতিটা তুলে নিল ফ্যাফ্যাসটা। ভয়ঙ্করভাবে কোপ দিল সুজানার বুকে। সুজানার রক্ত আর জাফরের রক্ত এক হয়ে মিশে গেল।
তীব্র গলায় বলল ফ্যাফ্যাস, ‘তুই আমার সন্তানকে বাঁচতে দিলি না! আমিও তোর সন্তানকে বাঁচতে দেব না!’
অসহ্য যন্ত্রণায় কেঁপে-কেঁপে উঠছে সুজানা। দিন-রাতের পার্থক্য ভুলে গেল সে। একটা বাচ্চার কোমল মুখ ফুটে উঠল তার চোখে। সুজানার মনে হলো, এটাই রোমি। আহা রে! কী সুন্দর ঝুঁটি করেছে মেয়েটা! চোখগুলো কেমন মায়া- মায়া! বড্ড আদর করতে ইচ্ছা করছে মেয়েটাকে!
ফ্যাফ্যাস এবং সুজানার দেহ পড়ে রইল মেঝেতে। এখনও মারা যায়নি তারা। সুজানার দেহ যেমন আস্তে-আস্তে অবশ হয়ে আসছে, ঠিক তেমনি ফ্যাফ্যাসের শরীরও শীতল হয়ে আসছে।
সুজানা চোখ মেলে তাকাল। বলল, ‘হে, আল্লাহ্! আমি মারা গেলেও আমার সন্তান যেন বেঁচে থাকে। তুমি আমার সন্তানকে বাঁচিয়ে দাও।
এই ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও সুজানার কেন জানি মনে হচ্ছে, কেউ তার ঘরে আসবে। তাকে হাসপাতালে নেবে, আর বেঁচে যাবে তার সন্তান।
সুজানার মত ফ্যাফ্যাসও কাতর স্বরে ভিন ভাষায় বলল, ‘হে, অন্ধকারের দেবতা! আমার সন্তানকে রক্ষা করো! তাকে এই পৃথিবীতে স্থান দাও!’
ফ্যাফ্যাস এবং সুজানা কারও প্রার্থনাই মঞ্জুর হলো না।
ফ্যাফ্যাস, এবং সুজানা একই সময়ে চিরতরে চোখ বুজল। এক শত বিশ বছরের জন্য পৃথিবীকে রক্ষা করেছে সুজানা। আবারও এক শ’ বিশ বছর পর অন্ধকার জগৎ থেকে পেটে ডিম নিয়ে পৃথিবীতে আসবে একটা ফ্যাফ্যাস। সে তার সন্তানদের জন্য খুঁজবে পোষক দেহ। হয়তো তখন পৃথিবীতে হবে ফ্যাফ্যাসের রাজত্ব। কিংবা সুজানার মত কেউ বুক আগলে রক্ষা করবে পৃথিবীকে।
ভয়
ছাদে কি নূপুর পায়ে কেউ হাঁটছে? নাকি অন্য কোনও শব্দ? আনোয়ার নিশ্চিত হতে পারছে না। এই শীতে বিছানা থেকে উঠতেও ইচ্ছা করছে না। যদিও ছাদে উঁকি দেয়া তার জন্য সহজ। কারণ সে ছাদের চিলেকোঠায় থাকে। এই বিশাল চারতলা বাড়িটা আনোয়ারদের। কিন্তু একা-একা শান্তিতে থাকার জন্য ও ছাদের চিলেকোঠাকেই বেছে নিয়েছে। ছাদেই যেন একটা সুন্দর সংসার আছে ওর। খুব প্রয়োজন না হলে আনোয়ার ছাদ ছেড়ে বাসায়ও তেমন একটা যায় না। তাই কেউ ওর সঙ্গে দেখা করতে এলে সরাসরি ছাদেই চলে আসে।
শব্দটা বেশ মিষ্টি লাগছে। এত রাতে ছাদে কে হতে পারে? ভাড়াটিয়াদের কেউ? কেয়া বা খেয়া নয় তো? দোতলার সোবহান সাহেবের দুই মেয়ে কেয়া আর খেয়া। কেয়া ইণ্টারমিডিয়েট পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির চেষ্টা করছে। আর খেয়া ক্লাস নাইনে পড়ে। দুই বোনই অসম্ভব রকমের সুন্দর। এরা প্রায়ই ছাদে আসে। সোবহান সাহেবের এ ব্যাপারটা একদম পছন্দ নয়। তাই তিনি ওদের ছাদে আসার বিষয়ে ১৪৪ ধারা জারি করেছেন। তবুও দুই বোনকে প্রায়ই ছাদে দেখা যায় এবং আনোয়ারের সাথে গল্প করাই যে তাদের মূল উদ্দেশ্য এটাও বোঝা যায়। আনোয়ারও ওদের খুব পছন্দ করে। বিশেষ করে কেয়াকে। পছন্দটা কোন্ পর্যায়ের এ ব্যাপারে আনোয়ার নিশ্চিত নয়। কেয়ার সাথে কথা বলতে ওর খুব ভাল লাগে এটুকুই ও জানে।
রাত ১টা ৫৫। এত রাতে কেয়া-খেয়ার যে-কারও ছাদে আসার সম্ভাবনা শূন্য। আর নূপুর পরে হাঁটার কথা তো চিন্তাই করা যায় না। আনোয়ার দরজা খুলে ছাদে এল। নূপুরের শব্দটা ক্ষীণ হয়ে আসে। তবে চমৎকার একটা ঘ্রাণ পায় আনোয়ার। আর মৃদু বাতাসে যেন শরীর জুড়িয়ে আসে। এমন কি হতে পারে ছাদে অশরীরী কিছু আছে? এমন হলে মন্দ হয় না। আনোয়ার এসব জিনিস দেখার জন্য অনেক অ্যাডভেঞ্চার করেছে। কত অদ্ভুত অভিজ্ঞতার যে মুখোমুখি হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।
আনোয়ারদের ছাদটা বেশ বড়। অনেক সুন্দর করে সাজানো। আনোয়ার ছাদে হাঁটতে শুরু করে। নূপুরের শব্দ আরও স্পষ্ট শোনা যায়। মনে হচ্ছে একটু দূরে কেউ যেন হাঁটছে। আনোয়ার দ্বিধাহীনভাবে ওদিকে হেঁটে যায়। হ্যাঁ, ওদিকে আসলেই কেউ আছে।
‘কে, কে ওখানে?’ আনোয়ার বলে ওঠে।
ওপাশে দাঁড়ানো মানুষটির হাঁটাহাঁটি বন্ধ হয়ে যায়। আনোয়ার মানুষটির আরও কাছে চলে আসে।
একটি মেয়ে। আপাদমস্তক বোরকায় ঢাকা। মুখে নেকাব।
‘কে আপনি?’ আনোয়ার প্রশ্ন করে বসে।
মেয়েটি আস্তে-আস্তে বলল, ‘আমি পরী।’
‘আপনার নাম পরী?’
‘না, আমি পরী। কোকাকে থাকি।’
‘মজা করছেন? আপনি চোর নাকি? এত রাতে এখানে? আপনার মতলব কী?’
‘এমনি ঘুরতে এলাম। আপনার সাথে গল্প করতে ইচ্ছা করছিল।’
ছাদের মৃদু আলোতে মেয়েটার হাতের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। নখগুলোতে নীল রঙের নেলপালিশ দেখতে পায় আনোয়ার।
মেয়েটা হাঁটতে-হাঁটতে ছাদের কিনারে চলে যায়। ওদিকে রেলিং নেই।
আনোয়ার শঙ্কিত মুখে বলল, ‘এই, কী করছেন? পড়ে যাবেন!’
মেয়েটার হাসির শব্দ শোনা গেল। আনোয়ারের মনে হলো কেয়া-খেয়া নয় তো! কিন্তু ও নিশ্চিত হতে পারছে না। মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করছে।
আনোয়ার বলল, ‘এই, আপনি কে বলুন তো?’
‘আমার নাম সুলেখা মিত্র।’
‘মিত্র? মানে আপনি তো হিন্দু! বোরকা পরেছেন কেন?’
‘কেন, কোনও হিন্দু কি বোরকা পরতে পারে না?’
উত্তর শুনে আনোয়ার অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।
মেয়েটি আবার বলল, ‘আসলে আমার সারা গায়ে রক্তের ছাপ, মাথার সামনের দিকটা থেঁতলে গেছে, মুখটাওঁ বেঁকে গেছে। এই জন্য নিজের চেহারা দেখাতে চাইছি না।’
‘মানে? কী বলছেন এসব? মজা করছেন?’
‘আপনার সাথে আর কথা বলব না। এখন আমাকে যেতে হবে। আপনি চোখ বন্ধ করুন।’
‘চোখ বন্ধ করব মানে?’
‘আমাকে যেতে হবে। সময় বেশি নেই। ওই যে দেখুন আকাশে কিছু একটা আসছে। সময় বেশি নেই।’
আনোয়ার আকাশের দিকে তাকায়। কিছু দেখতে পায় না। কয়েক মুহূর্ত পর পিছনে তাকিয়ে আনোয়ার দেখে মেয়েটা নেই।
সকালে ঘুম ভাঙার পর আনোয়ার ছাদে পায়চারী করতে থাকে। পাশের বাসা থেকে বেশ হইচই শোনা যাচ্ছে। কয়েকদিন আগে ওই বাড়ির কোনও এক মেয়ে মারা গেছে। আনোয়ারের সঙ্গে আশপাশের মানুষের খুব বেশি পরিচয় নেই। তাই সে ঠিক জানে না কে মারা গেছে। কেয়া-খেয়ার সঙ্গে কথা বললে অবশ্য জানা যেত।
সকাল ১১টার দিকে কেয়া ছাদে আসে। ওর হাতে আচারের বয়াম। আচারগুলো রোদে দিল কেয়া। আনোয়ারের দিকে তাকিয়ে মিষ্টি করে হাসল। ‘আনোয়ার ভাই, কেমন আছেন?’
‘এই তো, কেয়া, ভালই আছি।’
‘আপনার ঘোরাঘুরি কেমন চলছে?’
‘এই তো ভালই।’
‘এই যে আপনি ভূত-প্রেত খুঁজে বেড়ান, দেশের নানা জায়গায় যান, আপনার ভয় লাগে না?’
আনোয়ার হাসল। এরপর বলল, ‘মজা লাগে। অনেক মজা।’
‘আমাকে একবার আপনার সাথে নেবেন?’
‘অবশ্যই।’
‘আমার মাঝে-মাঝে কী ইচ্ছা করে জানেন? দূরে কোনও দ্বীপে চলে যেতে। যেখানে প্রকৃতির মাঝে পুরোপুরি হারিয়ে যেতে পারব।’
আনোয়ার হেসে বলল, ‘আশা করি তোমার ইচ্ছা একদিন পূরণ হবে।’
‘আপনি এমন করে হাসলেন কেন?’
‘সত্যি কথাটা কি জানো, আমাদের সবারই দূরে প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যেতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ইচ্ছাপূরণ হওয়ার পর দেখবে, বেশিদিন একা-একা ভাল লাগছে না।’
কেয়া জোর দিয়ে বলল, ‘আমার লাগবে।’
‘আচ্ছা মেনে নিলাম।’
তাদের কথোপকথনের এই পর্যায়ে পুলিসের গাড়ির সাইরেন শোনা গেল। আনোয়ার ছাদ থেকে নীচের রাস্তায় তাকাল। ওদের পাশের বাড়িতে পুলিস এসেছে।
আনোয়ার বলল, ‘কী ব্যাপার, হঠাৎ পুলিস কেন?’
‘আপনি কোন্ দুনিয়ায় থাকেন? কিছু জানেন না?’
‘না তো। কী হয়েছে?’
‘পাশের বাসার এক বৌদি দু’দিন আগে আত্মহত্যা করেছে।’
‘কীভাবে আত্মহত্যা করেছেন?’
‘ছাদ থেকে লাফ দিয়েছিল। মাথা থেঁতলে গেছে। খুব বিশ্রীভাবে মারা গেছে। পুলিস তার স্বামী আর শ্বশুরবাড়ির লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে।’
‘যিনি মারা গেছেন তাঁর নাম কী?’
‘সুলেখা বৌদি।’
আনোয়ার ভিতরে-ভিতরে বেশ চমকে উঠল। হঠাৎ বলল, ‘কাল রাতে কি তুমি বা খেয়া কেউ ছাদে এসেছিলে?’
‘রাতে! কী বলছেন এসব? রাত তো অনেক দূরের কথা, বাবা দিনের বেলাই ছাদে আসতে দিতে চান না। তো আপনি হঠাৎ এই প্রশ্ন করছেন কেন?’
‘না, এমনি।’
‘সুলেখা বৌদির স্বামী অনেক ক্ষমতাবান মানুষ। সুনীল কুমার বিশ্বাস। চেনেন তো তাকে? পুলিস, আণ্ডারওয়ার্ল্ডের মানুষ সবার সাথে তার ভাল সম্পর্ক। তাই এই আত্মহত্যায় তার কোনও ভূমিকা থাকলেও দেখবেন শেষ পর্যন্ত কিছুই হবে না।’
‘এটা আত্মহত্যা না হত্যা?’
‘আমি কী করে বলব বলেন। তবে আত্মহত্যাই মনে হয়। আত্মহত্যা হোক আর যা-ই হোক সুনীলের অত্যাচারেই নিশ্চয় এটা ঘটেছে।’
‘হুম।’
কেয়া চলে গেল। আনোয়ারের মনটা হঠাৎ খুব খারাপ হয়ে গেল। সারাদিন বাসায় কাটাল সে। আর রাতের খাবার শেষ করে ছাদের এক কোনায় বসে রইল। কিছু একটা নিয়ে বড্ড চিন্তিত সে বোঝা যাচ্ছে। রাত ১১টা ৪০ মিনিট। হঠাৎ একটা মিষ্টি গন্ধ পেল আনোয়ার। পিছনে ফিরে দেখল বোরকা পরা কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। আনোয়ার দ্রুত উঠে দাঁড়াল।
‘ভাল আছেন?’ মেয়েটির সরল জিজ্ঞাসা।
‘কে, কে আপনি?’ আনোয়ারের কণ্ঠে কিছুটা উত্তাপ।
‘আগের দিন তো বলেছি আমি সুলেখা।’
‘আমি বিশ্বাস করি না। আপনার মুখ দেখান।’
‘আপনি ভয় পাবেন।’
‘না, আমি ভয় পাব না।’
‘আপনি এখনই ভয় পাচ্ছেন। আপনার শরীর কাঁপছে।’
আনোয়ার আসলেই খুব ভয় পাচ্ছে। সে তো এত ভীতু নয়। তবে আজ কেন এমন হচ্ছে?
‘আপনি আমার কাছে কী চান?’
‘কিছু না। আপনার সাথে গল্প করতে চাই।’
‘আপনি চলে যান।’
‘বেশি কথা বলবেন না। চুপ করে বসুন। বেশি কথা আমার ভাল লাগে না।’ হঠাৎ হিংস্র গলায় বলল সুলেখা।
আনোয়ার বসে পড়ল।
‘আমি আপনাকে নিয়ে যেতে চাই,’ সুলেখা বলল। ‘মানে?’
‘আমার বড্ড একা লাগে। আপনাকে আমার চাই।’
আনোয়ারের মুখ আরও শুকনো হয়ে যায়। হেসে ওঠে সুলেখা। আনোয়ারের মনে হয় পরিচিত হাসি। কিন্তু সুলেখার হাসি তো ও আগে শোনেনি। সুলেখার হাতের দিকে চোখ যায় ওর। শক্ত করে কিছু ধরে রেখেছে সুলেখা। আনোয়ার বুঝতে পারে ওটা একটা ছুরি। ছাদে জ্বলতে থাকা বাল্বের মৃদু আলোতে হাতের লাল রঙের নেলপালিশও দৃশ্যমান হয়। আনোয়ারের শরীর কেমন যেন অসাড় হয়ে যায়। সুলেখাকে খুব ভয় পাচ্ছে ও।
‘আপনাকে আজ নেব না। চিন্তা নেই, তবে একদিন ঠিকই নিয়ে যাব। যান, এখন বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ুন।’
আনোয়ার বাধ্য ছেলের মত চিলেকোঠার ঘরে যায়। লাইট জ্বেলে বিছানায় বসে পড়ে। ১০ মিনিট পর বাইরে বেরিয়ে দেখে ছাদে কেউ নেই। তবে সেই মিষ্টি গন্ধটা আছে। যে গন্ধটার জন্য বারবার ওর চিন্তাশক্তি লোপ পাচ্ছিল।
সকাল ১০টায় ঘুম ভাঙল আনোয়ারের। রাতে বেশ ভাল একটা ঘুম হয়েছে। দ্রুত ফ্রেশ হলো আনোয়ার। বাসা থেকে কাজের ছেলে খালেদ ছাদে নাস্তা দিয়ে গেল। আনোয়ার নাস্তা শেষে কেয়াকে ফোন করল।
‘কেয়া, তুমি আর খেয়া কিছুক্ষণের জন্য ছাদে আসতে পারবে?’
‘কেন, আনোয়ার ভাই? হঠাৎ?’
‘একটু দরকার ছিল। খুব সমস্যা থাকলে আসার দরকার নেই। ‘
‘না, কোনও সমস্যা নেই। বাবাও বাড়িতে নেই। আমরা দশ মিনিটের মধ্যে আসছি।’
আনোয়ার আয়েশ করে সিগারেট ধরাল। আজ ওর মনটা বেশ ভাল। একটা রহস্যের সমাধান ও করতে পেরেছে বলে মনে হচ্ছে।
কেয়া-খেয়া কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাদে চলে এল। এই অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ পরিপাটি হয়ে এসেছে দুই বোন। আনোয়ারের ঘরে চেয়ারে বসল ওরা। কেয়া বলল, ‘কী, আনোয়ার ভাই। হঠাৎ জরুরি তলব?’
‘ভাল আছ তোমরা?’
‘হ্যাঁ, ভাল। আপনি তো কখনও ফোন করেন না। আজ হঠাৎ ফোন করে ছাদে আসতে বললেন?’
‘আমি ভণিতা পছন্দ করি না। তাই সরাসরি কিছু কথা বলতে চাই।’
আনোয়ারের কথা বলার ভঙ্গি দেখে ওরা দু’জনে চুপ হয়ে যায়। কিছু একটা আন্দাজ করে।
‘এটা কেন করলে তোমরা?’
‘কী করেছি?’ কেয়া মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল।
‘সুলেখা সেজে আমার সাথে কেন এমন করলে?’ দু’জনের মাথা নিচু হয়ে যায়।
‘উত্তর দিচ্ছ না কেন?’
‘আমরা আসলে আপনাকে একটু ভয় দেখাতে চেয়েছি।’
‘কেন?’
‘আপনি নিজেকে অনেক সাহসী ভাবেন। আসলেই সাহসী কি না সেটা দেখার জন্যই এমন করেছি।’
‘আমি প্রথম রাতে বুঝতে না পারলেও গতকাল রাতে হিসাব মেলাতে পেরেছি। প্রথম দিন কেয়া এসেছিল, আর দ্বিতীয় দিন খেয়া। ঠিক?’
‘কী করে বুঝলেন?’ পাল্টা প্রশ্ন কেয়ার।
‘কেয়া, তোমার হাতে নীল রঙের নেলপালিশ। আর খেয়ার হাতে লাল রঙের নেলপালিশ। আমি তোমাদের হাতের দিকে লক্ষ্য করেছিলাম।’
কথাগুলো শুনে কেয়া-খেয়া নিজেদের হাত ঢেকে ফেলল।
আনোয়ার আবার বলল, ‘তোমরা গায়ে এমন কোনও সুগন্ধি লাগিয়েছিলে, যেটা আমার চেতনার জগৎ ওলট-পালট করে দিয়েছিল। আমি সহজভাবে কিছু চিন্তা করতে পারছিলাম না। এজন্য ভয়টাও বেশ জেঁকে ধরেছিল। এই সুগন্ধি তোমরা পেলে কোথায়? আমার তো মনে হয় এটি নিষিদ্ধ কোনও সুগন্ধি। আর এটা শুধু ছেলেদের উপরই কাজ করে। আমি কি ঠিক বলেছি?’
‘হ্যাঁ, আপনি ঠিক বলেছেন। অনলাইনে একটা ওয়েবসাইটে বিজ্ঞাপন দেখে আমরা অর্ডার দিয়েছিলাম। তারা গোপনে আমাদের বাসায় দিয়ে গেছে। ওটা ছেলেদের আকৃষ্ট করতে ব্যবহার করা হয়।’
‘ওই সুগন্ধি এতটাই প্রখর ছিল যে আমি ঠিকভাবে চিন্তা করতে পারছিলাম না। আমি গলার স্বর শুনেও তাই তোমাদের চিনতে পারিনি। আচ্ছা, আমাকে ভয় দেখানো কি এতটাই জরুরি?’
কেয়া ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। আর খেয়ার চোখ-মুখ শক্ত হয়ে যায়।
কেয়া কাঁদতে-কাঁদতে বলল, ‘আমরা শুধু মজা করতে চেয়েছিলাম। প্লিজ, আমাদের মাফ করে দিন।’
কেয়ার জন্য মায়া হয় আনোয়ারের। ইচ্ছা করে মাথায় একটু হাত রাখতে। ইচ্ছাটাকে দমন করে আনোয়ার হাসল। এরপর বলল, ‘আমি রাগ করিনি। কান্না থামাও। বিষয়টা চিন্তা করে এখন বেশ মজাই লাগছে। তবে ঘটনার এখানেই ইতি ঘটাও। আর এসব কোরো না।’
দুই বোন মাথা নাড়ে। খেয়া নীচে চলে গেল। কেয়া বিছানায় বসেই থাকল। এখনও চোখে পানি ওর।
আনোয়ার আবার বিব্রত হলো। হঠাৎ বলল, ‘কেয়া, আমি একটু অন্যরকম। সৌন্দর্য বিষয়টা ভাল বুঝি না। কিন্তু তোমার কান্না দেখে মনে হচ্ছে স্বর্গের কোনও দেবী কাঁদছে। আমার ইচ্ছা করছে…’
কেয়ার কান্না পুরোপুরি থেমে গেল। চোখ বড়-বড় করে তাকাল আনোয়ারের দিকে। তারপর বলল, ‘কী ইচ্ছা করছে?’
‘নাহ। কিছু না।’
‘বলুন। বলতে হবে।’
‘তোমার চোখের পানি মুছে দিতে ইচ্ছা করছে।’
কেয়া দ্রুত এগিয়ে গেল। ‘দিন, চোখের পানি মুছে দিন।’
‘চোখে তো এখন পানি নেই!’
‘তা হলে কি আমাকে আবার কাঁদতে হবে?’
এ সময় খেয়া দৌড়তে দৌড়তে ছাদে এল। হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, ‘আপা, বাবা বাসায় এসেছে। তাড়াতাড়ি চলো।’
কেয়া-খেয়া দু’জনেই দৌড় দিল।
.
আজ সারাদিন বাইরে ঘুরে কাটিয়েছে আনোয়ার। নীলখেত থেকে কিছু বই কিনল। এক বন্ধুর সাথে পুরান ঢাকার রহস্যময় একটা বাড়ি নিয়ে আলাপ হলো, আনোয়ার সেখানে যেতে চায়। ওর বন্ধুও খুব আগ্রহ দেখাল। টিএসসি-তে গিয়ে কিছুক্ষণ একা-একা বসে রইল আনোয়ার। কয়েক বছর আগেও সে ঢাবির ছাত্র ছিল। এখন এখানের কাউকেই সে চেনে না।
রাত ৮টার দিকে বাসায় ফিরল আনোয়ার। প্রচণ্ড খিদে লেগেছে। বাসায় ঢুকেই পেট ভরে খেয়ে নিল ও। এরপর সোজা ছাদে। আকাশটা আজ বেশ পরিষ্কার। বাইরে বেশ বাতাস বইছে। আনোয়ার চিলেকোঠার ঘরে বসে একটা রগরগে ভূতের বই পড়ছে।
রাত ১২টা পার হয়ে গেছে। আশপাশের শব্দ কমে গেছে একদম। হঠাৎ ছাদে কারও পায়ের শব্দ শুনতে পেল আনোয়ার। পা টেনে-টেনে হাঁটার খস খস শব্দ। রুম থেকে বেরিয়ে আনোয়ার দেখতে পেল বোরকা পরা কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। কেয়া-খেয়া আবার ওকে ভয় দেখাতে এসেছে? মেজাজটা চরম খারাপ হলো ওর। এগিয়ে গেল ওদিকে।
আনোয়ার জোরে বলল, ‘তোমরা পেয়েছ কী? আবার ভয় দেখাতে এসেছ?’
বোরকা পরা মেয়েটি পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। আনোয়ারের কথায় তার কোনও ভ্রুক্ষেপ হলো না। আনোয়ার দ্রুত এগিয়ে গেল ওদিকে। টেনে মেয়েটাকে চোখের সামনে নিয়ে এল। এরপর টান দিয়ে নেকাব খুলে ফেলল। আজ একটা হেস্তনেস্ত ও করবেই।
নেকাব সরিয়ে আনোয়ার যেন পাথরের মত জমে গেল। সুলেখা মিত্র দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা একদিকে বেঁকে আছে, মাথার সামনে থেঁতলানো। ফোঁটা-ফোঁটা রক্ত পড়ছে সেখান থেকে। মুখটা অল্প খোলা। লালা ঝরছে সেখান থেকে।
আনোয়ার কয়েক পা পিছনে সরে গেল। ‘আ-আপনি?’
কোনও উত্তর নেই। সুলেখা মিত্র শুধু একদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। সে দৃষ্টি কোনও জীবিত মানুষের হতে পারে না।
‘কী চান আপনি?’
এবারও কোনও উত্তর নেই। আনোয়ার দ্রুত ঘরে ঢুকে পড়ল। দরজা বন্ধ করে দিল। সম্ভবত সে ভুল দেখছে। তার মস্তিষ্ক কোনও ধরনের খেলা খেলছে। আবার সেই পুরানো ভয়টা ফিরে এল আনোয়ারের। মনের ভিতর কাজ করছে তীব্র অপরাধবোধ। এক নিঃশ্বাসে দুই গ্লাস পানি খেল আনোয়ার। আবার ধীরে- ধীরে ছাদের দিকে উঁকি দিল। না, কেউ নেই সেখানে। কিন্তু আনোয়ার জানে সুলেখা আবার আসবে।
সে রাতে আর ঘুম হলো না ওর। সারারাত এপাশ-ওপাশ করল। কয়েকবার মনে হলো কে যেন দরজায় মৃদু শব্দ করছে। ছাদে দ্রুত গতিতে কেউ যেন হাঁটছে। কয়েকবার বাইরে বেরিয়েও আনোয়ার কাউকে দেখতে পেল না। দূরে কোথায় যেন একটা পাখি ডেকে উঠল।
.
সেই রাতের পর থেকে আনোয়ারের জীবনে হঠাৎ যেন দুর্যোগ নেমে এল। প্রতি রাতে সুলেখা ওর কাছে আসতে থাকে। কোনও-কোনও রাতে আনোয়ার ঘুম ভেঙে সুলেখাকে ওর বিছানায় দেখতে পায়। মাঝে-মাঝে চিৎকার করে ওঠে আনোয়ার। কখনও প্রচণ্ড ছটফট করতে থাকে। তখন সুলেখা চলে যায়।
সুলেখা আনোয়ারের সঙ্গে কোনও কথা বলে না। শুধু বিকৃত মুখমণ্ডল নিয়ে আনোয়ারের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। সেই তাকিয়ে থাকার মধ্যেই অনেক কথা লুকিয়ে থাকে। তার কিছুটা আনোয়ার ঠিকই বুঝতে পারে।
সেদিন রাতে সাহসে ভর করে আনোয়ার বলল, ‘কী চান আপনি?’
সুলেখা বিড়বিড় করে কিছু বলল। বোঝা যাচ্ছে ওর কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে।
আনোয়ার কাছে গিয়ে শোনার চেষ্টা করল। সুলেখা আবার বলল, ‘ক-কষ্ট অ-অ-অনেক ক-কষ্ট।’ রক্তের স্রোত যেন তুমুলবেগে নেমে এল সুলেখার মাথা আর মুখ দিয়ে। পানির একটা ধারাও গড়িয়ে পড়ল চোখ দিয়ে। আনোয়ার বুঝতে পারল সুলেখার কাছ থেকে মুক্তি পেতে হলে ওকে কী করতে হবে।
.
পর-পর তিন রাত না ঘুমিয়ে আনোয়ার কেমন যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে মাথার উপর রয়েছে অসহ্য চাপ। নিজেকে খুব অসহায় লাগতে থাকে ওর। সেই সাথে চলতে থাকে বিবেকের দংশন। আনোয়ার একটা সত্য সবার কাছ থেকে গোপন করেছে। সুলেখা আত্মহত্যা করেনি, ওর স্বামী সুনীল ওকে ছাদ থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছে। আনোয়ার সেদিন রাতে পাশের ছাদ থেকে পুরো দৃশ্যটা দেখতে পেয়েছিল। সুনীল সুলেখাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেই দৌড়ে নীচে চলে গিয়েছিল। পাশের ছাদ থেকে যে আনোয়ার ওদের দেখেছে এটা সুনীল জানে না। আর সেদিন আনোয়ারদের ছাদের বাতি ছিল নেভানো। তাই সুনীল ধারণা করেছে খুব সুচারুভাবে ও খুনটা করেছে। আসলে তা নয়। সুনীল জানে ওর যেটুকু ক্ষমতা তাতে বিষয়টা সহজেই আত্মহত্যা বলে প্রমাণ করা যাবে। আর কোনও প্রত্যক্ষদর্শী থাকার তো প্রশ্নই নেই। তাই ওর কোনও শাস্তি হবে না। আর সুলেখা যে মানসিক রোগী ছিল এ সংক্রান্ত ভুয়া কাগজপত্রও সুনীল জোগাড় করেছে। পুলিসও তদন্তে খুশি। সত্যি বলতে, সুনীল তাদের খুশি করে দিয়েছে। আর কিছুদিনের মধ্যেই পুলিস রিপোর্ট দেবে, সুলেখা মানসিক ভারসাম্যহীন ছিল। তাই সে আত্মহত্যা করেছে।
আনোয়ার পুরো বিষয়টা জেনেও চুপ ছিল। অনেক নির্ভার থাকার চেষ্টা করেছে। কারণ ও সুনীলের ক্ষমতা সম্পর্কে জানে। তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে গেলে ওর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা শূন্যের কোঠায় নেমে যাবে। আর তার সাক্ষ্যতে আদৌ কিছু হবে কি না, এ ব্যাপারেও সে সন্দিহান। তবুও নিজের কাপুরুষতা বারবার আনোয়ারের বিবেককে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। সুলেখা সুবিচার চাইতেই হয়তো বারবার ওর কাছে আসে। আনোয়ার এসব থেকে মুক্তি চায়। কাপুরুষ হিসাবে ও বাঁচতে চায় না। আনোয়ার ঠিক করল পুলিসের কাছে সে সব কিছু বলবে।
.
ছাদে দাঁড়িয়ে কেয়াকে সব খুলে বলল আনোয়ার। তার মত শক্ত চরিত্রের মানুষ কথা বলতে-বলতে হঠাৎ কেঁদে উঠল। বড্ড মায়া হলো কেয়ার। শক্ত করে জড়িয়ে রাখল আনোয়ারকে। কেয়া বলল, ‘আপনি, প্লিজ, শান্ত হোন। আমি আপনার পাশে আছি।’
আনোয়ার বলে, ‘আমি একজন মানুষের উপর অবিচার করেছি। একজন খুনির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারিনি।’
‘শুধু আপনি নন, অন্য যে-কোনও মানুষই এমন করত। আর সময় তো এখনও চলে যায়নি। আমি খেয়াকে বলেছি থানায় ফোন করতে। পুলিস কিছুক্ষণের মধ্যেই আসবে। আর এই যুদ্ধে আমি সবসময় আপনার পাশে আছি।’
কেয়া আবার বলল, ‘আপনার তো অনেক জ্বর। ইস্! চলুন, মাথায় পানি ঢালতে হবে।’
আনোয়ার বাধ্য ছেলের মত গেল। বিছানায় শুয়েই চোখ বন্ধ করল সে।
কত সময় পার হয়েছে জানে না আনোয়ার। হঠাৎ চোখ মেলে দেখল কেয়া ওর মাথায় পানি ঢালছে। একটু দূরে উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে আছে আনোয়ারের বাবা। আনোয়ার একটা ঘোরের মধ্যে আছে। সে সুলেখাকেও দেখতে পেল। লাল একটা শাড়ি পরেছে সুলেখা। কী সুন্দর করে সেজেছে ও! বিকৃত শরীরেও এখন তাকে সুন্দর লাগছে।
পুলিসের গাড়ির সাইরেন শুনতে পেল আনোয়ার। আবার ওর চোখ বন্ধ হয়ে এল।
বারবার চোখ মেলে কেয়ার উদ্বিগ্ন মুখ দেখে আশ্বস্ত হলো আনোয়ার। ও জানে এমন একটা মায়াবী মুখ ওকে সব বিপদ থেকে রক্ষা করবে।
অন্যায় যখন প্রতিপক্ষ
এক
মাঝে-মাঝে পরিবারের ভুল সিদ্ধান্তগুলো মেনে নেয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তবু সামাজিক জীব হিসাবে একজন মানুষকে অনেক কিছুই মেনে নিতে হয়। রনির একমাত্র ছোট বোন হীরা। রনির আব্বা আব্দুর রশিদ হুট করেই হীরার বিয়ে ঠিক করেছেন। বিয়ের বিষয়ে রনির মতামত জানারও প্রয়োজন বোধ করেননি। সব ঠিকঠাক করে আব্দুর রশিদ সেদিন ফোন করে রনিকে বললেন, ‘রনি, হীরার জন্য ভাল একটা পাত্র পেয়েছি। ফুলমণি গ্রামের ছেলে সিদ্দিকুর রহমান।’ একটু থেমে বললেন, ‘ছেলে ইণ্টার পর্যন্ত পড়েছে। গঞ্জে নিজের চারটা দোকান আছে, বাবার জায়গা-জমিও আছে বিস্তর। দুই-দুইটা পাকা দালান আছে তাদের। গ্রামেও খুব নাম-ডাক, সিদ্দিকুরের পরিবারকে সবাই এক নামে চেনে।’
রনি বলল, ‘হীরার এমন কী বয়স হয়েছে? বিয়ে নিয়ে এত তাড়াহুড়ো করছেন কেন?’
‘গত বছর যে মেয়ে ইন্টার পাশ করেছে, তার বিয়ে নিয়ে মা-বাবা চিন্তা করবে না?’ বিস্মিত গলায় আব্দুর রশিদ বললেন।
‘হীরার তো আরও পড়াশুনা করার ইচ্ছা। আমি চাই সে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুক,’ পাল্টা জবাব দিল রনি।
আব্দুর রশিদ ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, ‘মেয়েমানুষ অনেক পড়াশুনা করেছে। আর দরকার নেই। আমার মেয়ে শহরে গিয়ে মডার্ন মেয়ে হয়ে ঘুরবে, এটা আমি মেনে নিতে পারব না।’
‘আব্বা, ছেলেও তো তেমন ভাল না। পড়াশুনা তেমন করেনি, শুধু টাকা- পয়সা দেখেই রাজি হলেন?’
আব্দুর রশিদ রেগে গেলেন। থমথমে গলায় বললেন, ‘তোমার মতামত চাওয়ার জন্য আমি ফোন করিনি। আমার মেয়ের জন্য কোনটা ভাল, মন্দ, আমি বুঝব। তোমার এত মাথা ঘামাতে হবে না।’
‘ঠিক আছে, আব্বা।’
‘আগামী মাসের দুই তারিখে হীরার গায়ে হলুদ। তিন তারিখ বিয়ে। তুমি অবশ্যই আগে-ভাগে চলে আসবে।’
‘বড় ভাই হিসেবে আমার মতামতের যখন কোনও গুরুত্ব নেই, তখন আমি না আসলে কি কোনও ক্ষতি হবে?’
‘লাভ-ক্ষতির হিসাব আমাকে বোঝাবে না। আসবে কি আসবে না তোমার বিবেচনা।’
আব্দুর রশিদ ফোন রেখে দিলেন। পুরো বিষয়টা এখনও ঠিকমত মনের ভিতর সাজাতে পারেনি রনি। ঠিক সেই মুহূর্তে হীরা ফোন করল।
রনি ‘হ্যালো’ বলতেই ওপাশ থেকে হীরার কান্নার শব্দ শুনতে পেল।
রনি চমকে উঠে বলল, ‘কী হয়েছে, হীরা?’
‘আব্বা আমার বিয়ে ঠিক করেছে, শুনেছ?’
‘হ্যাঁ, শুনেছি।’
‘আমি এখন বিয়ে করব না, ভাইয়া।’
রনি কী বলবে বুঝতে পারছে না। তার মতামতের কোনও গুরুত্ব পরিবারে নেই। সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বলল, ‘কাঁদিস না। কেঁদে কোনও লাভ নেই।’
‘ভাইয়া, ভাইয়া, আমাকে বাঁচাও। আমি আরও পড়ালেখা করব।’
‘ধুর, বোকা। বিয়ে নিয়ে এত ভয় পাওয়ার কী আছে?’
‘আমি পড়ালেখা করতে চাই।’
দেখবি তোর বরই তোকে পড়ালেখা করাবে।’
‘না, করাবে না। লোকটা আমার চেয়ে বারো-তেরো বছরের বড়। তার বাবা বলেছে, আমার বউ না, একটা কাজের মেয়ে দরকার। ঘরের সবকিছু বাড়ির বউকেই সামলাতে হবে।’
‘এরপরেও আব্বা এই বিয়েতে রাজি হলেন?’
‘হ্যাঁ। আব্বারও মেয়েদের নিয়ে একই ধারণা। এ ছাড়া তিনি আমাকে একটা শিক্ষা দিতে চান। ‘
‘মানে? কী শিক্ষা?’
‘তুমি তো আনিস ভাইয়ার ব্যাপারটা জানতে। আব্বা আনিস ভাইয়ার ব্যাপারটা জানার পর তড়িঘড়ি করে বিয়ে ঠিক করেছেন।’
রনির মনে পড়ল। আনিস তাদের গ্রামেরই ছেলে। ওর চেয়ে কয়েক বছরের ছোট। এখন ঢাকা কলেজে মাস্টার্স ফাইনাল ইয়ারে পড়ছে। অনেক আগে থেকেই আনিস হীরাকে পছন্দ করে। হীরারও তার প্রতি আগ্রহ আছে। আনিস বলেছে একটা চাকরি জোগাড় করে হীরার বাসায় প্রস্তাব পাঠাবে। কিন্তু আব্দুর রশিদ এই বিষয়টা জানতে পেরে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠেছিলেন। তাঁর মেয়ের নিজ পছন্দে বিয়ে হবে, এটা তিনি চিন্তাও করতে পারেন না। ছেলে রাজপুত্র হলেও সেই বিয়ে তিনি মানবেন না।
ভাবলেশহীন গলায় রনি বলল, ‘আব্বার বিষয়ে কী আর বলব! তুই একটা ছেলেকে পছন্দ করিস তাতেই আব্বা এমন করছে। আর যদি প্রেম করতি, তা হলে মনে হয় মেরেই ফেলত।’
হীরা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, ‘ভাইয়া, আমি এখন কী করব?’
‘সাহস থাকলে পালিয়ে যা।’
‘সাহস নেই। আর পালিয়ে কোথায় যাব?’
‘আনিস কী বলে?’
‘তিনি তো খুব আঘাত পেয়েছেন। তাঁর বাবাকে দিয়ে আব্বার সাথে কথা রলানোর চেষ্টা করেছিলেন। আব্বা তাঁর সাথে ঠিকমত কথা তো বলেনইনি, উল্টো খুব অপমান করেছেন।’
‘আচ্ছা, দেখি আমি কী করতে পারি।’
‘তুমি দ্রুত বাসায় চলে এসো, ভাইয়া।’
‘আচ্ছা, আসব।’
‘আমার মন বলছে তুমি এলে কিছু একটা ব্যবস্থা হবে।’
দুই
দেরি করতে ইচ্ছে হলো না রনির। হীরার ফোন পাওয়ার কয়েকদিনের মধ্যেই অফিস থেকে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে গ্রামের উদ্দেশে যাত্রা করল। বোনের এই সমস্যায় হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। রনি গ্রামে যাওয়ার পর আব্বার হাসিমুখ দেখতে পেল। রনিকে দেখে তিনি বললেন, ‘ভাল সময়ে এসেছ। কাল সিদ্দিকদের বাসায় যাওয়ার কথা আছে। তোমাকে নিয়ে যাব।’
সিদ্দিকের সঙ্গে হীরার বিয়ে হতে যাচ্ছে।
রনি বলল, ‘আব্বা, আমি যাব না।’
মুহূর্তেই আব্দুর রশিদের মুখ কালো হয়ে গেল। বললেন, ‘কেন যাবে না?’
‘আব্বা, ছেলের বয়স তো অনেক বেশি। আমার চেয়েও চার-পাঁচ বছরের বড়।’
‘বয়সে বড় ছেলেই সংসার করার জন্য ভাল। এরা আবেগে চলে না। বুঝে- শুনে সিদ্ধান্ত নেয়।
‘কিন্তু হীরার তো এই বিয়েতে মত নেই।
‘হীরার যদি মত না থাকে সেটা আমার সামনে এসে বলতে বলো। দেখি কত সাহস!’ আব্দুর রশিদের হাত মুষ্টিবদ্ধ। তিনি যখন খুব বেশি রেগে যান, হাত মুষ্টিবদ্ধ করে রাখেন। রনির দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বললেন, ‘তোমার সাথে এই বিষয়ে আমি আর কোনও কথা বলতে চাই না। কাল তুমি আমার সাথে সিদ্দিকদের বাসায় যাবে, এটাই শেষ কথা। আর আমার সাথে কখনওই এমন উঁচু স্বরে কথা বলবে না।’
রনির ভিতরটা কেঁপে উঠল। আব্বার কথার বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস তার কখনওই ছিল না। কিন্তু আদরের বোনটার এই সমস্যা রনিকে কেমন যেন বদলে দিয়েছে। আব্বা যখন বলছেন তখন কাল সিদ্দিকুরদের বাসায় যাবে রনি। ছেলে কেমন এটাও তার জানা দরকার, আব্বার কথার উপর কোনও ভরসা নেই।
.
হীরার হবু বরের পুরো নাম সিদ্দিকুর রহমান। তার বাবার ভালই টাকা-পয়সা আছে বোঝা যাচ্ছে। পাশাপাশি বিশাল দুটো দোতলা বাড়ি। এই গ্রামে এমন আর একটাও বাড়ি আছে কি না সন্দেহ। রনিদের যে ঘরটাতে বসতে দেয়া হয়েছে তার সাজসজ্জা চোখে পড়ার মত। ঘরের মেঝেতে কার্পেট, দেয়ালে কিছু মহামানবের ছবি, শৌখিন সোফা আর ৩১ ইঞ্চি বিশাল এলইডি টিভি। দেখে কেউ বুঝতে পারবে না এটা গ্রামের কোনও বাড়ি। আব্দুর রশিদের মুখে বিজয়ীর হাসি। সম্ভবত তিনি ছেলেকে বোঝাতে চাইছেন, দেখো, কত বড় ঘরে হীরার বিয়ে ঠিক করেছি।
পাত্রপক্ষ যত্নের চূড়ান্ত করলেন। সিদ্দিকুর রহমান রনির চেয়ে বয়সে বড় হওয়া সত্ত্বেও তাকে ভাইয়া ডাকছে। রনি এতে কিছুটা বিব্রত বোধ করছে। সিদ্দিকুর রহমান মাথা নিচু করে বললেন, ‘আমার বউয়ের বড় ভাই মানে আমার বড় ভাই। এখানে বয়স কোনও বিষয় না। আমি বড় ভাইকে অবশ্যই সম্মান করব।’
সিদ্দিকুরের বাবাও বেশ কিছু কথা বললেন। বেশ অপরাধী মুখ করে বললেন, ‘এর আগের দিন আপনাদের একটা অন্যায় কথা বলেছিলাম।’
আব্দুর রশিদ বললেন, ‘কী কথা?’
‘বলেছিলাম, আমাদের একটা কাজের লোকের মত বউ দরকার। আমি অশোভন কথা বলেছিলাম। ক্ষমাপ্রার্থী। আসলে আমি খারাপ অর্থে কথাটা বলিনি। বুঝাতে চেয়েছি আমার ঘরের সব দায়িত্ব বউমার উপরেই থাকবে।’
আব্দুর রশিদ মাথা নেড়ে বললেন, ‘আমি কি এ বিষয়ে কোনও অভিযোগ করেছি, বেয়াই সাব?’
‘নাহ, আপনি কোনও অভিযোগ করেননি। তবে সিদ্দিকের মা সেদিন কথাটা শুনে খুব রাগ করেছিল। পরে আমারও মনে হয়েছে ভুল বলেছি।’
‘মেয়েদের বিয়ের পর অবশ্যই সংসারের কাজকর্ম করতে হবে। এটা তো চিরন্তন সত্য। আমার মেয়েও আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ্মী। সে সব সামলে নিতে পারবে।’
‘আর আমাদের কোনও দাবি-দাওয়া নেই। এমনকী মেয়েকে গয়না না দিলেও সমস্যা নেই। আমরাই সব দিয়ে মেয়ে সাজিয়ে আনব।’
‘এ তো আপনাদের মহত্ত্ব। তবে আমার একটা মাত্র মেয়ে। আমি সাধ্যমত মেয়েকে সবকিছুই দেব।’
‘ঠিক আছে। মেয়ের বাবার মনে আমরা কষ্ট দিতে চাই না। আর দেনমোহর আপনি যা ঠিক করবেন তাই। আমাদের কোনও আপত্তি নেই।’
আব্দুর রশিদ ছেলের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে বললেন, ‘এরা কত বড় বাড়ির মানুষ বুঝতে পেরেছ? পারলে এদের একবার সালাম করে দোয়া নিয়ো, জীবনে কাজে লাগবে।’
কথাবার্তা চলছে। হঠাৎ রনি বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন বোধ করল। সিদ্দিকুর নীচে গিয়েছে। সিদ্দিকুরের বাবা বাথরুমের কথা শুনে বললেন, ‘ভিতরে গিয়ে ডানদিকের মাথায় বাথরুম। নতুন টাইলস লাগিয়েছি। যাও।’
.
রনি ডানদিকে হাঁটতে লাগল। মনে হচ্ছে দোতলাতে তেমন কেউ থাকে না। বড়- বড় অনেকগুলো রুম। কিন্তু বেশিরভাগই তালাবদ্ধ। ঠিক বাথরুমের পাশের রুমটার সামনে গিয়ে রনি থমকে দাঁড়াল। রুমের দরজায় একটা বড় তালা ঝুলছে। কিন্তু মনে হচ্ছে ভিতর থেকে কারও কথার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কেমন যেন কৌতূহল হতে লাগল রনির। রুমের জানালাটা আলতো করে ধাক্কা দিল খুলে গেল সেটা। ভিতরটায় ঈষৎ অন্ধকার। বোঝা যাচ্ছে অনেক বড় একটা রুম। ভিতরে কোনও আসবাবপত্র নেই এবং মনে হচ্ছে রুমের মধ্যে কয়েকজন হাঁটাহাঁটি করছে।
হঠাৎ রনিকে চমকে দিয়ে একটা মেয়ে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। পরনে লাল রঙের শাড়ি। বড় আঁচল দিয়ে মুখটা ঢাকা। রনির মনের মধ্যে অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছে, মনে হচ্ছে কিছু একটা ঠিক নেই।
মেয়েটা বলল, ‘বোনের বিয়ে দিতে এসেছেন?’
‘জি।’
‘মিষ্টি এনেছেন তো?’
‘জি, এনেছি। আপনি কে?’
মেয়েটা হেসে উঠল। রনির মনে হচ্ছে আঁচলের ওপাশে একটা কিশোরী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
‘হাসছেন কেন?’
‘বিয়ে বাড়ি তো হাসিরই জায়গা।’
‘আপনি কে বললেন না তো।’
‘বলব না।’
‘ঘরের দরজায় তালা দেয়া কেন?’
‘আমি পাগল তো তাই আটকে রেখেছে।’ আবার হাসি
‘ওহ।’ রনি জানালা থেকে একটু দূরে সরে গেল। এতক্ষণে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। মেয়েটা সিদ্দিকুর রহমানের কোনও আত্মীয়। সম্ভবত মানসিক ভারসাম্যহীন তাই ঘরে আটকে রাখা হয়েছে।
রনি বাথরুমের দিকে যাচ্ছিল। মেয়েটা আবার ডেকে বলল, ‘যাবেন না। আপনার সাথে আরও কথা আছে।’
রনি মেয়েটার সঙ্গে কথা বলার তেমন কোনও আগ্রহ বোধ করছে না। পাগল মানুষ কখন কী করে, ঠিক নেই। মেয়েটা গলা নামিয়ে বলল, ‘সিদ্দিকের সাথে আপনার বোনের বিয়ে দেবেন না।’
‘কী বলছেন এসব? কেন?’
‘সিদ্দিকের সাথে বিয়ে না দিয়ে বোনকে পুড়িয়ে মেরে ফেলুন।’
মেয়েটা আসলেই পাগল, বোঝা যাচ্ছে। তার কথা জড়িয়ে যাচ্ছে।
‘আপনি কে?’ পুরানো প্রশ্নটা আবার করল রনি।
‘আমি আমেনা।’
‘ওহ।’
‘আমি সিদ্দিকের প্রথম বউ।’ আমেনার গলায় নিস্পৃহ ভাব।
‘অ্যা! সিদ্দিকুরের আগের বউ আছে? এটা তো জানতাম না। আপনি কি সত্যি বলছেন?’ নিজের বিস্ময়টা লুকাতে পারল না রনি।
‘হা-হা। আরও অনেক কিছুই আপনারা জানেন না।’
ঠিক সেই মুহূর্তে আরও একটা মেয়ে জানালার সামনে দাঁড়াল। এর পরনেও লাল রঙের শাড়ি। আগের মেয়েটার মত সে-ও আঁচল সামনের দিকে টেনে রেখেছে।
এই মেয়েটা নিজ থেকেই বলল, ‘আমি জমিলা। সিদ্দিকের দ্বিতীয় বউ।’
রনির মাথা ঘুরে উঠল। কী দেখছে এসব। সিদ্দিকের আগের বউ আছে। দু’জনেই পাগল? এটা কীভাবে হয়? নাকি এই মেয়ে দুটো মিথ্যা বলছে?
কিন্তু তাদের কণ্ঠস্বরের মধ্যে এক ধরনের বেদনার ছাপ রয়েছে, গভীর বেদনা নিয়ে মিথ্যা বলাটা কঠিন।
আমেনা বলল, ‘আমি সিদ্দিকের সাথে দুই বছর সংসার করেছিলাম। সিদ্দিকের মা-বাবা আর সিদ্দিক দিনরাত আমার উপর নির্যাতন করত। এরপর একদিন…’
‘একদিন কী?’
‘সিদ্দিক আর তার বাবা আমার সারা শরীরে অ্যাসিড ঢেলে দেয়। তারপর আমাকে এই রুমে ফেলে রাখে।’
রনি আঁতকে উঠল। ‘অ্যাসিড!!!’
‘হ্যাঁ। এদের গোপন কয়েকটা কারখানা আছে। সেখানে অ্যাসিড মজুত করে রাখা আছে। কাউকে শায়েস্তা করার দরকার হলেই এরা অ্যাসিডকে কাজে লাগায়।’
আমেনাকে থামিয়ে দিয়ে জমিলা বলল, ‘আমার দুই বছর সংসার করার সৌভাগ্য হয়নি। আমাকে গোপনে বিয়ে করে এনেছিল সিদ্দিক। বিয়ের তিন দিনের মাথায় বদমাশটা আমার শরীরে অ্যাসিড ঢেলে দেয়। আমাকেও এই রুমে ফেলে রেখেছিল। এমনভাবে লুকিয়ে রেখেছিল যে, গ্রামের লোকজনও সিদ্দিকের দ্বিতীয় বিয়ের কথা জানে না।’
‘আপনারা কী পাগলের মত কথা বলছেন? আপনারা বলছেন সারা শরীরে অ্যাসিড মেরে এখানে ফেলে রেখেছিল। তা হলে চিকিৎসা ছাড়া আপনারা বেঁচে আছেন কীভাবে?’
দু’জনেই ভয়ঙ্করভাবে হেসে উঠল। রনির হাতে-পায়ে শীতল ভাব ছড়িয়ে পড়ল। মনে হচ্ছে বহুদূর থেকে হাসির শব্দ ভেসে আসছে। জানালার সামনে থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করছে রনি। তবে অদ্ভুত কোনও আকর্ষণ তাকে সেখানে আটকে রেখেছে। কিছু একটা রনি দেখতে চায় না, কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে দেখতেই হবে।
ঘটনাটা ঘটল খুব দ্রুত। আমেনা এবং জমিলা এক ঝটকায় মুখের উপর থেকে আঁচল সরিয়ে নিল। রনির মুখ দিয়ে মৃদু আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল। রনি পিছনের দেয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়াল। বুঝতে পারছে তার শরীর কাঁপতে শুরু করেছে, ঘামে ভিজে গেছে শরীরের অনেকটা অংশ। এ ভয়ঙ্কর দৃশ্য রনি দেখতে চায় না। সে চোখ বন্ধ করল। মনে হলো, চোখ খুললেই দেখবে সামনের সবকিছু অদৃশ্য হয়ে গেছে। কিন্তু তা হলো না। সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা রনিকে বারবার দেখতে হলো।
রনি দেখল আমেনা এবং জমিলার মুখ, গলা, হাত ঝলসে গেছে। মুখমণ্ডলে চোখের কোনও অস্তিত্ব নেই, নাক এবং ঠোঁট যেন একসঙ্গে মিশে গেছে, কোথাও- কোথাও মাংস খসে পড়েছে, মাথায় চুল নেই একটাও।
জমিলা হেসে বলল, ‘বিশ্বাস হয়েছে আমাদের কথা? শরীরের সব জায়গায়ই এই অবস্থা। সব আপনাকে দেখাতে পারব না।’
রনি শক্ত করে দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে যে কোনও সময় মাথা ঘুরে পড়ে যাবে।
জমিলা বলল, ‘নিজের বোনের যদি এমন অবস্থা দেখতে চান, তবে অবশ্যই সিদ্দিকের সাথে বিয়ে দেবেন। তখন এই ঘরে আমরা তিনজন থাকব। মাঝে- মাঝে আমাদের তিনজনকে দেখে যাবেন।’
আমেনা গলা নামিয়ে বলল, ‘আমাদের কাছেও অ্যাসিড আছে। একদিন আমরাও সিদ্দিক আর ওর মা-বাবার উপর অ্যাসিড ঢেলে দেব।’
রনি আর দাঁড়াতে পারল না। বাথরুম সেরে দৌড়ে বসার রুমে ফিরে গেল। আব্দুর রশিদ রনির দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘কী হয়েছে? এভাবে ঘেমেছ কেন?’
রনি ঠিকভাবে বসতে পারছে না। তার মুখের মধ্যে শুকনো খটখটে হয়ে আছে। মনে হচ্ছে কথা বলার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছে।
‘চলো, আজ তা হলে উঠি,’ আব্দুর রশিদ রনির দিকে তাকিয়ে বললেন। রনি নিশ্চুপ। সবকিছু কেমন যেন এলোমেলো লাগছে।
সিদ্দিকুর রহমান আব্দুর রশিদের পা ছুঁয়ে সালাম করল। আব্দুর রশিদ চাপা গলায় বললেন, ‘দেখেছ কেমন ভদ্র ছেলে! মাশা’আল্লাহ।’
রনি দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল।
ফুলমণি গ্রাম থেকে রনিদের গ্রাম আশামণির দূরত্ব খুব বেশি নয়। ভ্যানে বা রিকশায় করে সবাই যাতায়াত করে। রনি আব্বাকে ভ্যানে তুলে দিয়ে বলল, ‘আব্বা, আপনি বাড়ি চলে যান। আমি একটু পর আসছি।’
‘কোথায় যাচ্ছিস?’
‘এই গ্রামে আমার একটা বন্ধু আছে। তার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি।’
‘আচ্ছা, যা। রাতে তুই বাসায় ফিরলে বিস্তারিত কথা বলব।’
তিন
অনেকদিন সেলিমদের বাসায় যায়নি রনি। পুরানো বন্ধুর সঙ্গে বহু বছর পর দেখা হলেও কোনও সমস্যা হয় না, আন্তরিকতায় এতটুকু খাদ থাকে না। সেলিম রনিকে দেখে আনন্দে জড়িয়ে ধরল। ওর মা-বাবার মুখেও হাসি ফুটল। রনি অনেকবার বলার চেষ্টা করল, ‘একটু পরেই চলে যাব।’ সেলিম কঠিন গলায় উত্তর দিল, ‘আজ যেতে পারবি না। পুকুরে জাল ফেলা হয়েছে। আর আব্বা মোরগ জবাই করবে। আজ রাতে তোকে ছাড়ছি না, আজ একসাথে খাওয়া-দাওয়া করব আর সারারাত পুকুর পাড়ে বসে গল্প করব।’
রনি রাজি হলো, মানে হতেই হলো। এরকম অকৃত্রিম ভালবাসাকে অগ্রাহ্য করা খুব কঠিন।
রাতের খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন দেখে রনি হতবাক হয়ে গেল। বড় রুই মাছ, দেশি কই, চিংড়ি, মোরগের মাংস, শিম ভর্তা, মসুরের ডাল, আচার এবং দই। এত অল্প সময়ে এত আয়োজন! শহরে কোনও আত্মীয়ের বাসায় এই ভালবাসার এক ভাগও কল্পনা করা যায় না। ‘আহা! গ্রামে যদি ফিরে আসতে পারতাম। পুরনো কত স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে।’ রনির মনের মধ্যে ঘুরতে লাগল কথাগুলো।
প্রিয় পুকুর ঘাটে অনেকদিন পরে বসেছে রনি আর সেলিম। হাতে পাতার বিড়ি। পাতার বিড়ি খাওয়ার মাধ্যমে তাদের পুরানো আনন্দ যেন আবার ফিরে এসেছে। সুন্দর বাতাসে শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। আর আকাশে চাঁদও রয়েছে। এত সুন্দর পরিবেশ যে তাদের মনে হচ্ছে অনন্তকাল এখানে বসে থাকে। নতুন- পুরানো নানা গল্প চলল দুই বন্ধুর। রনির কথা কতটা মনে পড়ে সেটাও জানিয়ে দিল সেলিম। কথায়-কথায় হীরার বিয়ের প্রসঙ্গটা তুলল রনি। প্রথমে বেশ আগ্রহ দেখালেও সিদ্দিকুর রহমানের কথা শুনে সেলিমের উৎসাহটা মিইয়ে গেল।
রনির দিকে না তাকিয়ে শুধু বলল, ‘তা হলে তোর বোনের সাথেই সিদ্দিক ভাইয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছে?’
‘তুই বিয়ের বিষয়ে আগেই জেনেছিলি?’
‘হ্যাঁ, শুনেছিলাম সিদ্দিক ভাই বিয়ে করতে যাচ্ছে। কিন্তু মেয়েটা যে আমাদের হীরা তা জানতাম না।’
‘হুম।’ আড়চোখে সেলিমের দিকে তাকিয়ে রনি বলল, ‘সিদ্দিকুর রহমান লোক কেমন?’
সেলিম রনির দিকে একনজর তাকাল। তারপরেই চোখ নামিয়ে নিল। মিনমিন করে বলল, ‘হ্যাঁ, ভালই তো।’
রনি সেলিমের কাঁধ ধরে বলল, ‘দেখ, সেলিম, এটা আমার বোনের জীবনের প্রশ্ন। তুই সিদ্দিকুর সম্পর্কে খারাপ, ভাল যা-ই জানিস, আমাকে বল। কিছু লুকাবি না।’
‘মানুষটা ভাল না রে,’ সরাসরি বলে বসল সেলিম। ‘যেহেতু বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে, তাই কিছু বলতে চাইছিলাম না।’
সেলিমের কথায় মনের মধ্যে ধাক্কা লাগলেও স্বাভাবিক গলায় রনি বলল, ‘বিয়ে শুধু ঠিক হয়েছে, হয়ে তো যায়নি। আমাকে সব খুলে বল।’
‘খুলে বলার খুব বেশি কিছু নেই। সিদ্দিকুর রহমানের বাবা খিজির রহমান গ্রামের প্রভাবশালী মানুষ। বহু মানুষের জমা-জমি দখল করে অনেক সম্পত্তির মালিক হয়েছে। সিদ্দিকুর রহমানও বাবার ধারা অব্যাহত রেখেছে। গ্রামের মানুষ এদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ।’
‘হুম।’
‘আর একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে সিদ্দিকুরের চরিত্রও তেমন ভাল না। গ্রামের বহু মেয়ের দিকে সে নজর দিয়েছে। তার জন্য অনেক মেয়েকে গ্রামছাড়া হতে হয়েছে। তুই কি জানিস সিদ্দিকুরের আগের একটা বিয়ে আছে?’
‘বলিস কী!’
‘হ্যাঁ, আমেনা নামে এই গ্রামের একটা অল্প বয়সী মেয়েকে বিয়ে করেছিল। একদিন জানতে পারলাম রান্নাঘরে আগুন লেগে আমেনা মারা গেছে। গ্রামের সবাই ছুটে গেলাম সিদ্দিকুরদের বাড়িতে। দেখলাম গোলপাতার রান্নাঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কাউকে লাশও দেখতে দেয়া হয়নি। তড়িঘড়ি করে বাড়ির পিছনের কবরস্থানে আমেনাকে কবর দেয়া হয়। আমেনার মৃত্যু নিয়ে লোকজনের মধ্যে নানান কানাঘুষা আছে।’
‘কী কানাঘুষা?’
এটা বলা ঠিক হবে না রে। মানুষ তো আজগুবি কথা বলতে পছন্দ করে। এগুলো বিশ্বাস না করাই ভাল।’
‘আমাকে বল, সেলিম। আমি অবুঝ মানুষ নই, কিছু শুনেই আমি হুট করে বিশ্বাস করে ফেলি না।’
নিচু গলায় সেলিম বলল, ‘অনেকে বলে সিদ্দিক এবং তার বাবা-মা মিলে আমেনাকে মেরে ফেলেছে।
‘ওহ, আল্লাহ!’
‘হ্যাঁ, তাদের ভাষ্য মতে আমেনাকে অ্যাসিডে পুড়িয়ে মারা হয়েছে। এরপর রান্নাঘরে আগুন লাগার নাটক সাজানো হয়েছে।’
রনি কী বলবে বুঝতে না পেরে সেলিমের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।
সেলিম আবার বলল, ‘সিদ্দিক এবং তার বাবা শত্রুদের অ্যাসিডে ঝলসে দেয়। অতীতে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে। তবে তারা এত ক্ষমতাশালী যে কেউ পুলিশের কাছে যেতে সাহস পায়নি। অনেক গুণ্ডা পোষে সিদ্দিকুর রহমান, পুলিশের সাথেও বেশ দহরম মহরম। বুঝতেই পারছিস।’
‘আচ্ছা, সিদ্দিকুর কি জমিলা নামে কোনও মেয়েকে বিয়ে করেছিল?’
সেলিম শক খাওয়ার মত চমকে উঠল। তার কথায় জড়তা চলে এল। ‘তু- তুই তু-তুই জ-জমিলার কথা কীভাবে জানলি?’
‘সত্যি কি না বল?’
‘জমিলাকে আমি কোনওদিন দেখিনি। গ্রামের কিছু মানুষ জমিলার কথাও বলত একসময়। সিদ্দিকুর নাকি দূরের এক গ্রাম থেকে ওই মেয়েটাকে বিয়ে করে এনেছিল। বিয়ের তিন দিনের মাথায় সে নিখোঁজ হয়েছিল। তবে জমিলাকে গ্রামের কোনও মানুষ চোখে দেখেনি। হতে পারে এটা একটা গুজব।’
‘আমি এখন কী করব, রে?’
‘আমিও তাই ভাবছি। হীরাকে সিদ্দিকুরের বউ হিসাবে দেখব ভাবতেই পারছি না।’
‘আব্বা এই পরিবার সম্পর্কে ঠিকমত খোঁজখবর না নিয়ে কীভাবে বিয়ে ঠিক করলেন?’
‘চাচাজান হয়তো খোঁজখবর নিয়েছেন। কিন্তু প্রকাশ্যে সিদ্দিকুরদের বিরুদ্ধে খারাপ কথা বলার সাহস কারও নেই।’
‘চল, শুয়ে পড়ি। ভাল লাগছে না।’
‘তোর মনটা খারাপ করে দিলাম!’
‘মনটা এমনিতেই খারাপ। তোর কথায় বরং আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। তুই যে আমাদের কত বড় উপকার করলি…’ সেলিমের হাতটা শক্ত করে ধরে বলল রনি।
সেলিম এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, ‘একটা অনুরোধ, আমি যে তোকে এসব বলেছি, কাউকে বলবি না।’
সেলিমের ভয়টা দেখে রনি বুঝতে পারল সিদ্দিকুর রহমান কতটা নিষ্ঠুর চরিত্রের।
চার
জীবনে প্রথমবারের মত আব্বার সঙ্গে কথা বলতে রনি কোনও ভয় পাচ্ছে না। বেশ স্পষ্ট স্বরেই বলল, ‘আব্বা, সিদ্দিকুর লোকটা ভাল না।’
২৩৮
আব্দুর রশিদ কঠিন চোখে রনির দিকে তাকালেন। ‘কী বললে?’
‘আপনি জানেন, সিদ্দিকুরের আগে বিয়ে আছে?’
‘হ্যাঁ, জানি।’
রনির মাথায় যেন বাজ পড়ল। ‘আপনি জানেন?!!’ উত্তেজনায় চেয়ার থেকে
দাঁড়িয়ে পড়ল।
‘এত লাফাচ্ছ কেন? জানি তো আগে একবার বিয়ে করেছিল। বউটা আগুনে পুড়ে মারা গিয়েছিল।’
‘আব্বা, সিদ্দিকুর আর তার বাবা-মা মিলে ওই বউটাকে মেরেছিল।’
‘একদম চুপ। বাজে কথা বলবে না।’
‘শুধু তাই নয়। আরও একটা মেয়েকে বিয়ে করে সিদ্দিকুর মেরে ফেলেছিল। গ্রামের অনেক মানুষের উপরে নির্যাতনের ইতিহাসও আছে ওদের। সিদ্দিকুরের চরিত্রও তেমন সুবিধার না।’
‘বাহ! এতদিন গ্রামে থেকে আমি কিছু জানতে পারিনি, আর তুমি দেখি এক রাতের মধ্যে সব কিছু জেনে গেছ!’
রনি আব্বার বিদ্রূপটা গায়ে না মেখে বলল, ‘কোনওভাবেই সিদ্দিকুরের সাথে হীরার বিয়ে দেবেন না, আব্বা।’
‘তুমি যা-যা বললে সব গ্রামের মানুষের রটনা। মানী লোক সম্পর্কে গ্রামের মানুষ খারাপ কথা ছড়াতে পছন্দ করে।’
‘আমি কোনওভাবেই এই বিয়ে হতে দেব না।’
আব্দুর রশিদ শক্ত করে চেয়ারের হাতল ধরলেন। তিনি রাগে অস্থির হয়ে আছেন বোঝা যাচ্ছে। বললেন, ‘সিদ্দিকুর একটা বিয়ে করেছিল। তার বউটা রান্নাঘরের আগুনে মারা গিয়েছিল। এটুকুই সত্যি। আর কিছুই সত্যি নয়। আর তুমি বিয়ে বন্ধ করার কে? এখনও আমার হাতে জোর আছে, মনে রাখবে। বেয়াদবকে সোজা করার উপায় আমার জানা আছে। আমার সামনে থেকে যাও।’
রনি উঠে দাঁড়াল।
‘তোমার শাস্তির ব্যবস্থা আমি অবশ্যই করব। আমি দুষ্ট গরু পুষতে চাই না।’
রনি মনে-মনে বলল, ‘আপনার গোয়ালে আমি আগুন দেব, আব্বা। আপনার গোয়াল শুধু শূন্যই থাকবে না, ধ্বংসও হয়ে যাবে। আপনার অত্যাচার অনেক সহ্য করেছি, আর না।’
পুরানো একটা দুঃখের স্মৃতি মনে পড়ে গেল রনির। রনির বয়স যখন আঠারো, তখন আব্বা তার বিয়ে দিয়েছিলেন। একরকম বাধ্যই করেছিলেন বিয়ে করতে। আব্দুর রশিদের যুক্তি ছিল অল্প বয়সে ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিলে তাদের জীবন সুখের হবে। কিন্তু রনির জীবন সুখের হয়নি। রনির বারো বছর বয়সী বউ শাহানা আব্দুর রশিদের পরিবারের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেনি। তবে রনির কেন যেন মনে হয়, শাহানা তাকে একটু-একটু পছন্দ করত। বাসর রাতে সে অনেক গল্প করেছিল। তার জীবনের গল্প। তাদের বাসার গাভীটার একটা নতুন বাছুর হয়েছিল, বাছুরটা তার গলা শুনলেই দৌড়ে আসত। তার বান্ধবী সীমা নাকি মাছের মত সাঁতার কাটে, কোনও ছেলেও তাকে হারাতে পারবে না। রিয়াজ- শাবনূরের নতুন সিনেমাটা দেখে নাকি চোখে পানি এসে যায়। রনির সে-রাতে মনে হয়েছিল, আল্লাহ শুধু তার জন্য এই বিশেষ মেয়েটিকে তৈরি করেছেন। শাহানার মধ্যে রনি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল।
কিন্তু সুখ রনির ভাগ্যে ছিল না। বিয়ের পরদিন থেকে আব্দুর রশিদের কড়া শাসনের মধ্যে পড়ে গেল শাহানা। রনির আম্মা এমনিতে আব্দুর রশিদের কাছে কোনও কাজে পাত্তা পান না। তবে আব্দুর রশিদ যখন কারও প্রতি অন্যায় করেন, তখন রনির আম্মা তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে যান। সে অর্থে তিনিও একজন নিষ্ঠুর মানুষ।
রনির আব্বা, আম্মা দু’জনে মিলে শাহানার জীবনটা বিষিয়ে দিয়েছিলেন কিশোরী মেয়েটা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কাজ করত। কাজের পুরস্কার হিসাবে ছিল শ্বশুরের ধমক আর শাশুড়ির টিপ্পনী। তার খাওয়া-দাওয়ার দিকেও কারও নজর ছিল না। তার পোশাক-আশাক ছিল চাকরানির মত। অবাক ব্যাপার হচ্ছে শাহানা কখনও রনির কাছে এ বিষয়ে প্রতিবাদ করেনি। প্রতিবাদ করলেও অবশ্য রনির কিছু করার ছিল না।
শাহানার পরিবারের সদস্যরা এই নির্যাতনের বিষয়ে সবই জেনেছিল। তারা ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেনি। ফলে, দুই মাসের মধ্যেই তালাক সম্পন্ন হয়েছিল। রনি শুনেছে শাহানার আবার বিয়ে হয়েছে। একটা বাচ্চাও নাকি আছে। লজ্জার ব্যাপার হচ্ছে, এখনও রনি আনমনে সেই কিশোরী মেয়েটার কথা ভাবে। গোলগাল মুখ, মিষ্টি চেহারা, চোখে-মুখে কৌতূহল ভরা যে মেয়েটাকে দেখে রনি মুগ্ধ হয়েছিল।
তালাক হয়ে যাওয়ার কয়েক বছর পর, আব্দুর রশিদ আবার রনির বিয়ের চিন্তা করেছিলেন। কিন্তু রনি কোনওক্রমেই রাজি হয়নি। রনির নিজের জীবনে যে খারাপ বিষয়টা ঘটে গেছে, তা সে কোনওক্রমেই হীরার জীবনে ঘটতে দেবে না, কিছুতেই না।
পাঁচ
আনিস ঢাকা থেকে গ্রামে এসেছে। হীরাই সংবাদটা রনিকে দিয়েছে। রনি দেরি না করে আনিসদের বাসায় গেল। আনিসদের বাসা কাছাকাছি। রনিকে দেখে আনিস কিছুটা ভড়কে গেল। কোনওকিছু নিয়ে শঙ্কায় ভুগছিল হয়তো। রনি তার সব শঙ্কা, দূর করে বলল, ‘তোমার আর হীরার বিষয়টি আমি জানি।’
আনিসের মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল।
রনি বলল, ‘এখন কী করবে ভাবছ?’
‘ভাইয়া, আমার তো তেমন কিছু করার নেই। চাচা না চাইলে তো কেউই কিছু করতে পারবে না।’
‘কোনওকিছুতে জয়ী হতে চাইলে জেদ থাকা প্রয়োজন। আব্বা যতটা না রাগী, তার চেয়ে বেশি জেদি। তাঁর এই জেদের জন্যই জীবনে সব বিষয়ে তিনি সফল। আমার মনে হয় তাঁর বিরুদ্ধে কেউ মাথা তুলে দাঁড়ালে তিনি হতভম্ব হয়ে যাবেন।’
‘ভাইয়া, আমাকে কী করতে বলছেন?’
‘আগে নিজের মনকে প্রশ্ন করো, হীরাকে তুমি বিয়ে করতে চাও কি না?’
‘ভাইয়া, অবশ্যই চাই। হীরা আমার জীবনে না এলে হয়তো সবই হারিয়ে ফেলব।’
‘তা হলে নিজেই ভেবে বলো, তোমার কী করা উচিত।’
‘আমি সবকিছু করতে রাজি আছি। কিন্তু হীরা কি চাচার মুখোমুখি দাঁড়াতে পারবে?’
‘হীরা আর তুমি ঢাকায় চলে যাও। এরপর সেখানে বিয়ে সেরে নাও। যদিও আমি চেয়েছিলাম হীরার বিয়েটা আরও কয়েক বছর পর হোক। কিন্তু পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে তোমাদের বিয়ে করে নেয়াই ভাল। বিয়ের পর আমার বাসাতেই তোমরা থাকবে। তুমি চাকরির চেষ্টা করবে আর হীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নেবে।’
আনিস আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়ল। ‘ভাইয়া, আপনি…’ আনিসের চোখে পানি দেখতে পেল রনি। পুরুষমানুষের চোখে পানি অনেক বড় ব্যাপার। রনির মনে হচ্ছে, এই ছেলেটার কাছে তার বোন সুখেই থাকবে।
রনি বলল, ‘আনিস, মন নরম করলে চলবে না। অনেক বড় মানসিক শক্তি দরকার তোমাদের।’
‘ভাইয়া, আমি শক্তই আছি। আমার অনেক স্বপ্ন। সংসারের কথা চিন্তা করে আমি ছোটখাট সঞ্চয় করেছি। সে সঞ্চয় এখন তিন লাখ টাকা হয়েছে।’
‘খুবই ভাল। এত টাকা কীভাবে জমালে?’
‘আমি প্রচুর টিউশনি করি। টিউশনির টাকাই একটু-একটু করে জমিয়েছি।’
‘খুব ভাল। ওই টাকাটা এখন খরচ কোরো না। চাকরি পাওয়ার আগ পর্যন্ত ওই টাকায় হাত দেবে না।’
‘জি, ভাইয়া।’
‘দু’দিনের মধ্যে তোমরা ঢাকা যাবে। আমার বাসার ঠিকানা দিয়ে দিচ্ছি। বাসার চাবিটাও মনে করে নিয়ে নিয়ো।’
‘আপনি আমাদের সাথে যাবেন না?’
‘নাহ, এখনই যাব না। আমি এদিকটা সামলাব। দেখব আব্বা কী করেন। ওনাকেও তো সামলাতে হবে।’
‘আচ্ছা, ভাইয়া।’
‘আমি হীরাকে সব বলব আজকে। তুমি তৈরি থেকো।’
.
পরিস্থিতি মানুষকে সাহসী করে দেয়। রনি ভেবেছিল হীরা আব্বার সিদ্ধান্তের বাইরে যেতে ভয় পাবে, কিন্তু তাকে বিষয়টা বুঝিয়ে বলতে সহজেই রাজি হয়ে গেল। আব্বার প্রতি তার ক্ষোভও দীর্ঘদিনের।
রনি বলল, ‘কিছু জামা-কাপড় গুছিয়ে রাখিস। আর এই চার হাজার টাকা রাখ। সোজা আমার বাসায় যাবি। একটা বেডরুম খালি পড়ে আছে, তোদের থাকতে কোনও সমস্যা হবে না।’
হীরার মুখটা শুকনো। মুখের সেই চিরাচরিত হাসিটা যেন নিভে গেছে।
রনি ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলল, ‘ভয় লাগছে?’
‘হ্যাঁ, ভাইয়া, লাগছে। যদি আব্বা জানতে পারেন, তা হলে…’
‘আমি নিজে তোদের ঢাকার বাসে উঠিয়ে দিয়ে আসব। রাত এগারোটার বাসে যাবি। এই সময় কেউ জেগে থাকবে না।’
.
সহজে হয়ে গেল সবকিছু। রাত এগারোটার বাসে হীরা আর আনিসকে উঠিয়ে দিয়েছে রনি। হীরা খুব কাঁদছিল। বেচারী খুব ভয় পাচ্ছিল। যদিও বড় ভাই ওর পাশে আছে, তবু এত বড় সিদ্ধান্ত নেয়া সহজ নয়। যতই আশ্বস্ত করা হোক না কেন, বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া একটা মেয়ের জন্য অনিশ্চিত যাত্রার মত। রনি আনিসকে অনেকবার বলেছে যেন হীরাকে দেখেশুনে রাখে। এই মেয়েটা শহরের পরিবেশ সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না।
ছয়
রাতে বাসায় ফিরতে-ফিরতে প্রায় একটা বেজে গিয়েছিল রনির। সারারাত ঘুমাতে পারেনি। শুধু এপাশ-ওপাশ করেছে। শেষ রাতের দিকে নিজের অজান্তেই চোখটা একটু বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তার।
রনির ঘুম ভাঙল আব্বার চেঁচামেচি শুনে। আব্দুর রশিদ রনির ঘরের দরজায় সজোরে লাথি দিচ্ছিলেন। রনি ধড়মড়িয়ে উঠে বসল। আব্বা কি তবে সব জেনে গেছেন?
আব্দুর রশিদ চিৎকার করছেন, ‘দরজা খোল, হারামজাদা।’
রনি শান্তমুখে দরজা খুলে দিল।
আব্দুর রশিদের মুখ ক্রোধে লাল হয়ে আছে। তাঁর চোখ দিয়ে যেন আগুন ঝরছে। হাতে একটা ধারাল দা চকচক করছে। রনির ভয় পাওয়া উচিত। কিন্তু ও অবাক হয়ে লক্ষ করল তার ভয় করছে না। আব্দুর রশিদ দা উঁচু করে বললেন, ‘শুয়োরের বাচ্চা, বল, হীরা কোথায়?’
‘ঢাকায় গেছে, আব্বা।’
‘ওর নাগরের সাথে গেছে? তুই ওদের পাঠিয়েছিস, না?’
‘হ্যাঁ।’
‘ওই হারামজাদী চিঠি লিখে গেছে। কী সুন্দর সেই চিঠির ভাষা।’ দাঁতে-দাঁত চেপে আব্দুর রশিদ বললেন, ‘আজ তোকে টুকরো-টুকরো করে কুকুরকে খাওয়াব।’
‘আপনার সাহস থাকলে আমাকে কোপ দেন।
‘কী বললি?’
‘বলেছি আপনার সাহস নেই আমাকে কোপ দেয়ার। আছে শুধু হম্বিতম্বি।’ আব্দুর রশিদ অবাক দৃষ্টিতে রনির দিকে তাকিয়ে রইলেন। মনে হচ্ছে তিনি নিজের ছেলেকে চিনতে পারছেন না।
রনি সোজাসুজি আব্বার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘সিদ্দিকুর একটা খুনি। সে তার আগের দুই বউকে খুন করেছে। গ্রামের মানুষকে বহু বছর ধরে তারা নির্যাতন করে আসছে। এমন একটা পরিবারে আমি আমার বোনকে বিয়ে দিতে পারব না। আপনি বাবা হিসাবে ব্যর্থ হতে পারেন, আমি ভাই হিসাবে ব্যর্থ হতে পারব না।’
আব্দুর রশিদ যেন সংবিৎ ফিরে পেলেন। রনি তাঁর চোখে অন্য দৃষ্টি দেখতে পেল। তিনি হারতে চান না। এবার বোঝা যাচ্ছে তিনি সত্যিই রনিকে কোপ দেবেন। আব্দুর রশিদ চিৎকার করতে-করতে রনির দিকে এগিয়ে আসছেন। ও অপেক্ষা করছে। ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যাওয়ার অপেক্ষা। ঠিক সেই মুহূর্তে রনির আম্মা এবং পাশের বাড়ির ইব্রাহিম কাকা ঘরে ঢুকলেন। আব্দুর রশিদকে চেপে ধরলেন তাঁরা। তিনি তখন পশুর মত শব্দ করছেন, মুখ দিয়ে লালা ঝরছে। বলছেন, ‘ছেড়ে দাও। আমাকে ছেড়ে দাও। এই শুয়োরকে মেরে আমি একটা পুণ্য করতে চাই।’
আম্মা চিৎকার করে বললেন, ‘রনি, তুই চলে যা। তোর আল্লাহর দোহাই লাগে তুই চলে যা।’
আম্মা আর ইব্রাহিম কাকা শক্ত করে ধরে রেখেছেন আব্দুর রশিদকে। তিনি ক্রমাগত চিৎকার করে যাচ্ছেন। রনি ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। না, আব্বার ভয়ে নয়। এমন ক্রমাগত চিৎকার করলে আব্বা অসুস্থ হয়ে পড়বেন, তখন নিজেকে বড্ড দায়ী মনে হবে।
রনিদের বাসায় প্রচুর মানুষ জড় হয়েছে। সবাই মজা দেখতে এসেছে। আব্দুর রশিদ চিৎকার করে বললেন, ‘আজ থেকে আমার কোনও ছেলে-মেয়ে নেই। আমি দুই কুত্তাকেই ত্যাজ্য করলাম।’
রনি মনে-মনে বলল, ‘আপনার এই দোজখে আর ফিরতে চাই না।’
পরিশিষ্ট
হীরা আর আনিসের বিয়ে পিছিয়ে দিয়েছে রনি। হীরা তার বাসায়ই আছে। ঢাকার একটা কলেজে অনার্সে ভর্তি হয়েছে। প্রস্তুতি ভাল না হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে চান্স হয়নি।
আনিস মাস্টার্স পাস করেছে। আগের মত মেসেই থাকছে। ঠিক করেছে একটা ভাল চাকরি পেয়েই হীরাকে বিয়ে করবে। আব্বা-আম্মা রনি এবং হীরার কোনও খোঁজ নেয়ার চেষ্টা করেননি। এমনকী একবার ফোনও করেননি। তবে গতকাল সেলিম রনিকে ফোন করেছিল। সে এমন একটা খবর দিল যে রনি হতবাক হয়ে পড়ল। তার ভাষাতেই বলা যাক:
‘তুই হীরাকে ঢাকা পাঠিয়ে দিয়েছিস আগেই জেনেছিলাম। এসব ব্যাপার নিয়ে দুই গ্রামে নানা কথাবার্তা চলছিল। তবে বেশিরভাগ মানুষই বলেছে, ‘যাক, ভালই হলো। মেয়েটা সিদ্দিকুরের হাত থেকে বেঁচে গেল।’ কেউ-কেউ অবশ্য পুরো ঘটনায় মজাও লুটছে। সিদ্দিকুর আর তার বাবা তোদের বাসায় এসে অনেক চেঁচামেচি করেছিল। তারা এর শেষ দেখে নেবে এ-ও বলেছিল। কিন্তু এক সপ্তাহ আগে আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। গভীর রাতে কেউ সিদ্দিকুর এবং তার মা-বাবার উপর অ্যাসিড ঢেলে দিয়ে গিয়েছিল। সিদ্দিকুরের মা-বাবাকে বাঁচানো যায়নি। সিদ্দিকুর কোনওমতে প্রাণে বেঁচে গেলেও তার চোখ, কান, শ্বাসনালীসহ শরীরের বিভিন্ন জায়গা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সিদ্দিকুর আর কোনওদিন চোখে দেখবে না, কানেও শুনবে না। এমনকী এখনও সে ঠিকমত কথাও বলতে পারে না। হাসপাতালেই আছে এই সাত দিন। বারবার কী যেন বলার চেষ্টা করে। তার ভাঙা-ভাঙা কথা শুনে মনে হয় লাল শাড়ি পরা দুটো মেয়ে তাদের উপর অ্যাসিড ঢেলেছে। সেই মেয়েদের শরীরে নাকি অসুরের মত শক্তি। অনেক সময় নিয়ে তারা অ্যাসিড ঢেলেছে। গ্রামের মানুষ এ ঘটনায় খুবই খুশি। সবাই মেয়ে দুটোকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে।’
রনি বিড়বিড় করে বলল, ‘ধন্যবাদ, আমেনা এবং জমিলা।’
আঁধারে বসতি
আমি একটা অন্ধকার জায়গায় শুয়ে আছি। যতবার চোখ মেলে তাকাই, কিছু দেখতে পাই না। প্রচণ্ড একটা ভয়ের অনুভূতি আমায় জাপটে ধরে। জায়গাটা আশ্চর্যরকম নীরব। আমি খুকখুক করে কেশে উঠলাম। মনে হলো কাশির শব্দ বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল। আমি কি মারা গেছি? নাকি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি? আমি সম্ভবত কোনও মাঠে শুয়ে আছি। আস্তে-আস্তে উঠে বসলাম। আমাকে খুব ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করতে হবে। আমি কীভাবে এখানে এলাম? আচ্ছা, এমন কি হতে পারে যে, বন্ধু মাহমুদ আমাকে খারাপ কিছু খাইয়ে দিয়েছে? হয়তো আমি নেশার ঘোরে আছি। মাহমুদের আবার উল্টাপাল্টা জিনিস খাওয়ার অভ্যাস আছে।
আমি মারা যাইনি, এটা বেশ বুঝতে পারছি। হাত-পা ইচ্ছামত নাড়াতে পারছি। একটা মশা ভয়াবহ কামড় দিল। ব্যথা পেলাম। চারপাশে কেমন একটা কটু গন্ধ পাচ্ছি। মারা গেলে বা স্বপ্ন দেখলে এসব অনুভূতি কাজ করার কথা না। কিন্তু জায়গাটা এত অন্ধকার কেন? আমি চিৎকার করে বললাম, ‘কেউ আছেন?’
কেউ জবাব দিল না। মনের ভিতর ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যাচ্ছে। এত ঘুটঘুটে অন্ধকারে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। হঠাৎ একটা আশঙ্কা আমায় পেয়ে বসল। আমি হয়তো অন্ধ হয়ে গেছি। তাই কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু হুট করে অন্ধ হলাম কী করে? না, হিসাব মিলছে না। খিদেও পেয়েছে বেশ। চোখের সামনে নান আর মুরগির গ্রিলের ছবি ভাসছে। প্রায় প্রতি রাতেই আমি নান আর মুরগির গ্রিল খেয়ে থাকি। সঙ্গে কড়া লিকারের এক কাপ চা।
না, এভাবে বসে থাকা সম্ভব না। আমি আবার বললাম, ‘কেউ আছেন?’
গম্ভীর গলায় কেউ জবাব দিল, ‘হ্যাঁ, আছি।’
‘কে আপনি?’
‘আমি কেউ না।’
‘আমি কোথায় আছি?’
‘নিজেই বুঝতে পারবে।’
‘আমি কি বেঁচে আছি?’
‘না।’
‘তবে মারা গেছি?!!’
‘না। মারা যাওনি।’
‘মানে?!!’
‘শান্ত হও। সব বুঝতে পারবে।’
‘আমি কি স্বপ্ন দেখছি?’
‘হতে পারে এটা এক ধরনের স্বপ্ন। আবার না-ও হতে পারে।’
‘আমার ভয় করছে। প্রচণ্ড ভয়।’
‘ভয় পাওয়াই স্বাভাবিক। আরও অনেক কিছু তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।’
‘আপনি কি আমার হাতটা একটু ধরবেন?’
‘না।’
‘এত অন্ধকার কেন?’
‘একটু পরে অন্ধকার কমে যাবে।’
‘তাই?!’
‘হ্যাঁ। তুমি সবকিছু আবছা দেখতে পাবে।’
‘এই অন্ধকার পুরোপুরি দূর হবে কখন?’
‘এই অন্ধকার পুরোপুরি দূর হবে না।’
‘আমাকে বাঁচান।’
‘হা-হা-হা।’
‘ভয় লাগছে…আমার ভয় লাগছে।’
‘মাটিতে শুয়ে পড়ো।’
‘কেন?’
‘যা বলছি করো।’
আমি শুয়ে পড়লাম।
লোকটা আবার বলল, ‘একটু পরে অন্ধকার কমে যাবে। তুমি সবকিছু আবছা দেখতে পাবে। তখন মাটি থেকে উঠে পড়বে। এরপর হাঁটতে শুরু করবে।’
‘হেঁটে কোন্দিকে যাব?’
‘সেটা তোমাকেই ঠিক করতে হবে।’
‘আপনি আমার সাথে থাকবেন?’
‘না।’
‘প্লিজ, আমাকে সাহায্য করুন।’
কোনও উত্তর পাওয়া গেল না।
আমি চিৎকার করে বললাম, ‘সাহায্য করুন। আমাকে সাহায্য করুন। বাঁচাও, আমাকে কেউ বাঁচাও!’
কেউ সাড়া দিল না। আমি কাঁদতে লাগলাম। সর্বশেষ কবে কেঁদেছি মনে নেই। আর আজ ভয়ে-আতঙ্কে যেভাবে কাঁদছি, তার সঙ্গে অতীতের কোনও কান্নার মিল নেই।
ভয়! ভয়! ভয় আমাকে ক্রমাগত গ্রাস করছে। আমি বারবার সৃষ্টিকর্তার কাছে প্রার্থনা করছি: ‘হে, মহান প্রতিপালক! সাহায্য করো। আমাকে রক্ষা করো।’
কিছুক্ষণ পর চারদিকে একটা পরিবর্তন লক্ষ করলাম। আস্তে-আস্তে চারদিক একটু পরিষ্কার হচ্ছে। আমি একটু আশ্বস্ত হলাম। আমি একটা ছোট খোলা জায়গায় শুয়ে আছি। আমার চারপাশে অসংখ্য গাছপালা। তা হলে আমি কি কোনও বনের মধ্যে আছি? আমি উঠে পড়লাম। ভেবেছিলাম যেদিকে আলোর রেখা দেখব সেদিকে এগোব। কিন্তু চারদিকে ভাল করে তাকিয়ে আমি কোনও আলোর রেখা দেখতে পেলাম না। সোজা এগোতে শুরু করলাম। চারদিকে ঘন জঙ্গল। কিন্তু জঙ্গলটা ভয়ঙ্কর নীরব। কোনও পশুপাখির ডাক শুনতে পাচ্ছি না। এমনকী ঝিঁঝিও ডাকছে না। কিছুক্ষণ একটানা হাঁটার পর আমি আবার একটা ফাঁকা জায়গা পেলাম। পা খালি হওয়াতে আমার হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। বিশ্রাম নেয়ার জন্য ফাঁকা জায়গাটায় বসলাম। হঠাৎ মনে হলো, একটু দূরে কেউ একজন বসে আছে। আমি এগিয়ে বললাম, ‘কে? কে ওখানে?’
‘আমি।’
‘আমি কে?’
‘আমার কোনও নাম নেই।’
‘কী করছেন এখানে?
‘বৃদ্ধ হয়েছি তো, পরিশ্রম সহ্য হয় না, তাই বিশ্রাম নিচ্ছি।’
‘এটা কোন্ জায়গা?’
‘এটা তোমার জন্য একটা নতুন জগৎ।’
‘আমি বুঝতে পারছি না।’
‘পৃথিবীর কোনও-কোনও মানুষকে এ জগতে আসতে হয়।’
‘কী বলছেন এসব!!’
হ্যাঁ। তবে সবাই এ জগৎ থেকে ফিরে যেতে পারে না। তাদের চিরদিনের জন্য এ জগতে থাকতে হয়!’
‘আপনিও কি আটকে পড়া একজন?’
‘না।’
‘তবে আপনি কে?’
‘আমি এ জগতের পাহারাদার!’
‘পাহারাদার?!!’
‘হ্যাঁ।’
‘আমি কিছু বুঝতে পারছি না।’
‘তোমার বোঝার প্রয়োজন নেই।’
‘আমি খুব ভয় পাচ্ছি। আপনি একটু কাছে এলে আমার ভয়টা একটু কমত।’
‘না, আমি কাছে আসব না।’
‘ঠিক আছে, আমিই কাছে আসছি।’
বড় আলখাল্লায় লোকটির পুরো শরীর ঢাকা। আমি তাঁর হাত-পা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু মুখ দেখতে পাচ্ছি না। আমাকে আসতে দেখে তিনি একটু দূরে সরে গেলেন। বললেন, ‘না, না, কাছে এসো না।’
আমি কথা না শুনে দৌড়ে এসে লোকটির হাত ধরলাম। হাতটা ছাড়ানোর চেষ্টা করলেন তিনি। তখন একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটল। লোকটির হাত খুলে গেল। হাতটা আমার হাতে ঝুলছে। আমি ঝটকা মেরে হাতটা ফেলে দেয়ার চেষ্টা করলাম।
পাহারাদার বৃদ্ধ বললেন, ‘আমার হাতটা তোমাকে দিয়ে দিলাম।’ বৃদ্ধ হাসতে লাগলেন।
হাতটা আমার গলা চেপে ধরল। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এল আমার। কোনওমতে বললাম, ‘বাঁচাও…
একটু পর হাতটা আমার গলা ছেড়ে দিল। বৃদ্ধ বললেন, ‘বেশি কৌতূহল ভাল নয়। বুঝলে?’
আমার শরীর কাঁপুনি দিচ্ছে। দৌড় দিতে চাইলাম। কিন্তু হাত-পা কেমন যেন অসাড় হয়ে গেছে। চিৎকার করে বললাম, ‘ভূত-ভূত…আ-আপনি ভূত।’ বৃদ্ধ বিরক্তিমাখা কণ্ঠে বললেন, ‘না, আমি ভূত নই। আমি পাহারাদার।’
‘আ-আপনার হাত…হা-হাত…’
‘চুপ করো। শুধু হাত কেন, আমার শরীরের সব অংশই টান দিলে খুলে আসে।’
‘অ্যা!!!’
‘হুঁ। এই দেখো।’ বৃদ্ধ তাঁর অন্য হাত দিয়ে পা দুটি খুলে ফেললেন। আমার পেটের ভিতর কিছু যেন পাক দিয়ে উঠল। বৃদ্ধ আবার বললেন, ‘দাঁড়াও, এবার মাথাটা খুলি।’
‘না…না…না। থামুন, থামুন।’ আমি দৌড় দিলাম।
বৃদ্ধের হাত-পা আলাদা-আলাদাভাবে আমাকে ধরতে এগিয়ে আসতে লাগল। জঙ্গলের ভিতর দিয়ে দৌড়াচ্ছি। কখনও পড়ে যাচ্ছি, ব্যথা পাচ্ছি। তবু থামছি না। একটা ভয়ঙ্কর হাসি শুনতে পেলাম। কেউ জোরে বলে উঠল, ‘বোকা, তুমি খুব বোকা।’
মনে হলো বৃদ্ধের গলা। কিন্তু আশপাশে কোথাও তাঁকে দেখতে পেলাম না। প্রচণ্ড তৃষ্ণা পেয়েছে। মনে হচ্ছে পানি খেতে না পারলে আর এক মুহূর্তও বাঁচব না। এমন সময় কেউ বলল, ‘অ্যাই।’
‘কে?’
‘আমি। এই তো এদিকে।’
আমি একটা ছোট বাচ্চা মেয়ের অবয়ব দেখতে পেলাম। তবে মেয়েটির মুখ দেখা যাচ্ছে না। মেয়েটি আস্তে-আস্তে বলল, ‘পানি খাবে?’
‘হ্যাঁ।’
‘এই নাও।’ মেয়েটি আমার দিকে একটা পানির পাত্র এগিয়ে দিল।
আমি ঢকঢক করে পানি খেয়ে নিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, ‘তুমি এখানে কী করছ?’
‘আমি আমার মাকে খুঁজছি।’
‘তোমার মা কোথায়?’
‘হারিয়ে গেছে।’
‘তুমি পানি পেলে কোথায়?’
‘সামনে অনেক পানি।’
‘সামনে কোথায়?’
‘ওই তো সামনে।’
‘তুমি এখানে এলে কীভাবে?’
‘আমি সবসময় এখানেই আছি।’
‘তুমি এখানকার সবকিছু চেনো?’
‘হ্যাঁ। চিনি।’
‘আমি এখান থেকে বেরোতে চাই। কোনদিকে যাব?’
‘নদীর দিকে যেতে হবে।’
‘নদীটা কোথায়?’
‘বলব না।’
‘তোমার মা-ও কি এখানে থাকতেন?’
‘হ্যাঁ। হঠাৎ করেই হারিয়ে গেছে।’
‘নদীটা কোথায় বললে, আমি তোমার মাকে খুঁজে দেব।’
‘মিথ্যা! তুমি মিথ্যা বলছ! তুমি জানো না আমার মা কোথায়।’
‘জানি। আমি জানি।’
‘জানো না। তুমি মিথ্যা বলছ,’ মেয়েটি চিৎকার করে উঠল। ‘তোমার শাস্তি পেতে হবে। মিথ্যাবাদীকে শাস্তি পেতে হয়।’
এমন সময় কিছু একটা আমার মুখে আঘাত করল। প্রচণ্ড আঘাত। দুটো দাঁত ছিটকে বেরিয়ে এল। মুখ দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল। আমি পড়ে গেলাম।
মেয়েটি আবার চিৎকার করে বলল, ‘আমি মিথ্যা ঘৃণা করি। ঘৃণা… ঘৃণা!’
প্রচণ্ড যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছি। ক্ষুধা, তৃষ্ণাও আগের থেকে বহুগুণ বেড়ে গেছে। কতক্ষণ পেরিয়েছে জানি না। দু’ঘণ্টা? পাঁচ ঘণ্টা? নাকি অনন্ত সময়? আমি আবার উঠলাম। হাঁটতে শুরু করলাম। মুখের ব্যথা ক্রমেই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। এমন সময় একটা মেয়ের কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। আমি ভয়ে- ভয়ে বললাম, ‘কে?’
একটু সামনেই এক তরুণী মেয়েকে দেখতে পেলাম। এখানে যাদের সাথে আমার দেখা হয়েছে, কারও মুখই আমি দেখতে পাইনি। তবে আবছা আলোতে এই মেয়েটির মুখ দেখতে পাচ্ছি। অন্ধকারটা বেশ চোখে সয়ে গেছে। মেয়েটি আমাকে দেখে চমকে উঠল। বলল, ‘কে? কে আপনি?’
‘আমি? আমি নিয়াজ। আপনি কে?’
‘আমি রূপা। আপনি কীভাবে এলেন এখানে?’
‘আমি জানি না।’
‘আমিও বুঝতে পারছি না, কীভাবে এখানে এলাম।’
‘কতক্ষণ হলো আছেন এখানে?’
‘জানি না। সময় আন্দাজ করতে পারছি না। হয়তো একদিন, দু’দিন কিংবা আরও বেশি।’
‘এতদিন!! কোনও খাবার কি পেয়েছেন?’
‘হ্যাঁ, এখানে মাটিতে অনেক ধরনের ফল পড়ে আছে, সেগুলো খেয়েছি। সামনে একটা ডোবা আছে, সেখান থেকে পানি খেয়েছি।’ বলতে-বলতে রূপা কেঁদে উঠল। ‘আমি বাঁচতে চাই। ঘরে ফিরে যেতে চাই।’
আমি রূপার হাত ধরলাম। রূপার কান্না স্তিমিত হয়ে আসতে লাগল।
আমি বললাম, ‘আপনার কি অতীতের সবকিছু মনে আছে? কোথায় থাকতেন আপনি?’
‘হ্যাঁ। সবকিছু মনে আছে। আমি উত্তরাতে থাকি।
‘আমারও সবকিছু মনে আছে। পরিবারের কথা, বন্ধুদের কথা।’
‘কী হবে এখন আমাদের?’
‘আমাদের নদী খুঁজে বের করতে হবে।’
‘তারপর?’
‘হয়তো নদী পেরোতে হবে আমাদের।’
‘আপনাকে কে বলেছে?’
‘আমি জেনেছি।’
‘আপনি মানুষ তো?’
এত বিপদের মধ্যেও আমি হেসে বললাম, ‘হ্যাঁ, রূপা, আমি মানুষ।
‘প্লিজ, আপনি আমাকে ছেড়ে যাবেন না।’
‘না, যাব না। আমার নিজেরই খুব ভয় লাগছে! আপনাকে দেখে একটু হলেও মনে সাহস ফিরে পেয়েছি।’
‘আচ্ছা, এমন কি হতে পারে এটা মৃত্যুর পরের কোনও জগৎ?’
‘আমি ঠিক জানি না, রূপা। তবে সম্ভবত আমরা মারা যাইনি।’
‘তা হলে এটা কোন জায়গা?’
‘আমি ঠিক জানি না। হতে পারে এটা অন্ধকার জগৎ।’
‘অন্ধকার জগৎ?’ রূপার কণ্ঠে আতঙ্ক।
‘হ্যাঁ। তবে যে করেই হোক আমাদের এখান থেকে বেরোতে হবে।’
‘পারব আমরা?’
‘নিশ্চয়ই পারব।’ রূপাকে দেখে আমার মনোবল বহুগুণ বেড়ে গেছে। নারী যে প্রেরণাদায়ী তা এখানে এসেও টের পাচ্ছি।
আমরা এগোতে লাগলাম। রূপা আমার হাতটা শক্ত করে ধরে রেখেছে। বিচিত্র কোনও শব্দ শুনলেই আমাকে জড়িয়ে ধরছে। মনে হচ্ছে আমি যেন তার কত আপন। আমরা হাঁটতে লাগলাম। হাঁটতেই লাগলাম। চেষ্টা করছি সোজা হাঁটতে। কিন্তু দিক ঠিক রাখা খুব মুশকিল হয়ে যাচ্ছে।
এমন সময় মনে হলো কিছু একটা আমাদের অনুসরণ করছে। ভয়ে আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। চেঁচিয়ে বললাম, ‘কে? কে ওখানে?’
হঠাৎ একটা জন্তু আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। জন্তুটাকে একবার কুকুর, একবার বাঘের মত লাগছে। জন্তুটা আমাকে ধারাল নখ দিয়ে আঁচড় দিতে লাগল। যেন আমার উপর ভয়ঙ্কর আক্রোশ রয়েছে। কামড় দিয়ে আমার শরীরটা ক্ষতবিক্ষত করে ফেলল জন্তুটা। রূপা কোথা থেকে একটা কাঠ জোগাড় করে জন্তুটাকে আঘাত করল। পালিয়ে গেল ওটা। আমার শরীরের বিভিন্ন জায়গা থেকে রক্ত ঝরছে। মনে হচ্ছে মারা যাব। ভয়ঙ্কর আর্তনাদ করে চলেছি। রূপা কাঁদছে। কী করবে বুঝতে পারছে না। ওর একটা হাত আমার মুখের উপর দিয়ে রেখেছে। বলল, ‘খুব যন্ত্রণা হচ্ছে?’
এমন সময় কেউ একজন আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগলেন। এই লোকের মুখও দেখা যাচ্ছে না। তিনি কিছু পাতা আমার গায়ের উপর ফেললেন। রূপাকে ইঙ্গিত করে বললেন, ‘পাতা থেকে রস বের করে ওর গায়ে লাগিয়ে দাও। ক্ষতগুলো ঠিক হয়ে যাবে।’
রূপা ভয়ার্ত গলায় বলল, ‘কে আপনি?’
‘যা বলছি, আগে তাই করো।’
রূপা পাতাগুলো পিষে যতটুকু সম্ভব রস বের করল। এরপর আমার শরীরের ক্ষতস্থানগুলোতে লাগিয়ে দিল। একটু পরেই টের পেলাম ব্যথা কমে গেছে। উঠে বসলাম। বললাম, ‘আপনাকে ধন্যবাদ।’
‘তুমি অনেক বড় অন্যায় করেছ। এজন্য জন্তুটা তোমাকে আক্রমণ করেছে।’
‘কী অন্যায়?’
‘অন্যায়টা তুমি ভাল করেই জানো। দু’দিন আগে কি ঘটেছিল তোমার মনে নেই?’
আমি চমকে উঠলাম। মনে আছে। স্পষ্ট মনে আছে।
কাঁপা গলায় বললাম, ‘আপনি কে?’
‘আমি পথনির্দেশক বৃদ্ধ। আমি মানুষকে এখান থেকে বেরোনোর পথ বলে দিই।’
‘সত্যি! বলুন, কীভাবে আমরা বেরোব?’
‘বলব। নিশ্চয়ই বলব।’
‘আমি এখানে কতক্ষণ ধরে আছি?’
‘এখানে সময় বলে কিছু নেই।’
‘মানুষ এই জগতে আসে কীভাবে?’
‘ঘুমের ঘোরে, কোমায় থেকে, জ্ঞান হারিয়ে এ জগতে চলে আসতে পারে। আমরা যদি দুটো জগৎ ধরি-বাস্তব জগৎ এবং অন্ধকার জগৎ, তা হলে একজন মানুষকে একটা নির্দিষ্ট সময়ে অন্ধকার জগৎ থেকে বাস্তব জগতে ফিরে যেতে হয়। নতুবা সে চিরদিনের জন্য এ জগতে আটকা পড়ে যায়।’
‘আপনিই তো বললেন এখানে সময় বলে কিছু নেই। তা হলে কোন্ নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলছেন?’
অন্ধকার জগতে সময় বলে কিছু নেই। কিন্তু বাস্তব জগতে তো আছে, আমি বাস্তব জগতের সময়ের কথা বলছি।’
‘বাস্তব জগতের কোন্ সময়ের মধ্যে আমাদের এখান থেকে বেরোতে হবে?’
তোমার হাতে এখনও যথেষ্ট সময় থাকলেও মেয়েটির খুব বেশি সময় নেই। মাত্র বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে এখান থেকে বেরোতে হবে।’
রূপা ভয়ঙ্কর চমকে উঠল
আমি বললাম, ‘কেউ কি এই অন্ধকার জগৎ থেকে বাস্তব জগতে ফেরত গেছে?’
‘হ্যাঁ, কতজনই তো ফিরে যায়।’
‘আচ্ছা। কেউ বাস্তব জগতে গিয়ে কি আবার অন্ধকার জগতে ফিরে আসতে পারে?
‘যে মানুষ একবার অন্ধকার জগৎ থেকে বাস্তব জগতে যায়, সে মনেপ্রাণে চাইলে আবার অন্ধকার জগতে ফিরে আসতে পারে। তখন তাকে আবার পথ খুঁজে বেরিয়ে যেতে হবে।’
‘এবার আপনি আমাদের বেরোনোর পথ বলে দিন।’
‘তোমরা সোজা. আর একটু হাঁটলেই একটা ফাঁকা জায়গা পাবে। সেখান থেকে ডান দিকে যেতে থাকবে। এরপর একটা ছোট খাল পাবে। খালে পানি খুব কম। খাল পেরিয়ে আবার সোজা এগোতে থাকবে। দেখবে নদীর ঘাটে পৌঁছে গেছ। সেখানে এক মাঝিকে পাবে। তাকে রাজি করিয়ে তোমাদের ওপারে যেতে হবে। ওপারে যাওয়ার পর টানা হেঁটে যেতে হবে সোজা। খুব বেশিক্ষণ নয়। দুই-তিন ঘণ্টা। কিন্তু মানুষ হাঁটতে পারে না। ওই পথ জুড়ে হাজার-হাজার কাঁটা রয়েছে। অনেকেই ওই পথে কিছুটা গিয়েই বসে পড়ে। দেরি করে ফেলে। কেউ উঠে দাঁড়ানোর শক্তি হারিয়ে ফেলে। কেউ ভুল পথে চলে যায়। কেউ ব্যথায়, যন্ত্রণায় ঘোরের মধ্যে চলে যায়। এদিকে সময় শেষ হয়ে যায়। চিরতরে আটকা পড়ে যায় সে।’
বৃদ্ধ পথনির্দেশক একটু থামলেন। আবার বললেন, ‘তোমরা যদি ঠিক পথে এগোতে থাকো তবে একসময় তীব্র আলোর রেখা দেখতে পাবে। সেই আলোর দিকে কিছুক্ষণ এগোলেই তোমরা বাস্তব জগতে চলে যাবে।’
‘ধন্যবাদ। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাহায্য করার জন্য। আমরা এখনই এগোতে চাই।’
‘হ্যাঁ, যাও।’
আমরা এগোতে লাগলাম। ওই পথনির্দেশক বৃদ্ধ সাহায্য না করলে হয়তো গোলকধাঁধায় আটকা পড়তাম। হয়তো এক জায়গাতেই ঘোরাঘুরি করতাম। রূপা এখন আমার আরও কাছে। এত কাছে যে ওর নিঃশ্বাসের উষ্ণতা শরীরে অনুভব করছি। বাস্তব জগতে এমন হত কি না জানি না। তবে এখানে খুব সহজেই কথাটা বলে ফেললাম রূপাকে
‘রূপা, আমরা যদি ফিরে যেতে পারি, তবে…’
‘তবে কী?’
‘তুমি-আমি চিরকাল পাশাপাশি থাকব।’
‘হ্যাঁ, তুমি-আমি…. চিরকাল…একসাথে।’
ভালবাসায় আমার হৃদয়টা আর্দ্র হলো। মনে হলো সব ভয়কে জয় করা সময়ের ব্যাপার। আমরা নদীর ঘাটে পৌঁছলাম। নদীতে তীব্র স্রোত। নদীর দিকে তাকাতেই বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। পাগলের মত মাঝিকে খুঁজতে লাগলাম। এমন সময় রূপা আমাকে বলল, ‘ওই যে, একটা নৌকা।’
অন্ধকারে ভাল দেখা যায় না। তবে নৌকা বলেই মনে হচ্ছে। আমরা নৌকায় ওঠার চেষ্টা করতেই নৌকার মাঝি বলল, ‘কে তোমরা? কী চাও?’
‘আমরা ওপারে যেতে চাই। আমাদের পার করে দিন।’
‘এখন পার করতে পারব না।’
‘দয়া করুন। আমাদের পার করে দিন।’
অনেক অনুনয়-বিনয়ের পর মাঝি রাজি হলো। আমরা দু’জন নৌকায় উঠে বসলাম। নৌকা চলতে শুরু করল। তীব্র স্রোতে দুলতে শুরু করল।
রূপা বলল, ‘নৌকা ডুবে যাচ্ছে… ডুবে যাচ্ছে। আমরা মারা যাব।’
মাঝি জবাব দিল, ‘না। নৌকা ডুববে না। আর এ জগতে কেউ মারা যায় না। তোমরা এখন চোখ বন্ধ করো। আমি না বলা পর্যন্ত চোখ খুলবে না।’
‘কেন?’
‘এত কৌতূহল ভাল নয়। যা বলছি করো।’
আমরা চোখ বন্ধ করলাম। তখনই নৌকাটা আরও বিচিত্রভাবে দুলতে লাগল। চারদিকে নানান শব্দ শুনতে পেলাম। কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে, কেউ বিচিত্র ভাষায় কিছু বলছে। মাঝির কণ্ঠও শুনতে পেলাম: ‘যা-যা, দূর হয়ে যা।’
কেউ বলল: ‘পার করে দে। আমাদের পার করে দে।’
‘যা-যা…নৌকায় উঠবি না। যা, দূর হ।’
‘পার করে দে…’ প্রচণ্ড আর্তনাদ শুনতে পেলাম। সে আর্তনাদ আকাশ- বাতাস ভেদ করে চলে গেল।
রূপা ফিসফিস করে বলল, ‘আমরা কি ফিরতে পারব? এখান থেকে মুক্তি পাব?’
‘নিশ্চয়ই মুক্তি পাব, রূপা, নিশ্চয়ই।’
যতবার রূপাকে আশ্বাস দিলাম ততবারই বুকের ভিতরটা ওলটপালট হয়ে গেল আমার। কিছুক্ষণ পর মাঝি বলল, ‘চোখ খোলো।’
আমরা চোখ মেলে তাকালাম। মনে হলো নদীর এপারে পৌঁছে গেছি। মাঝি বলল, ‘যাও, নেমে পড়ো।’
আমি বললাম, ‘আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।’
‘তোমার ধন্যবাদ আমার প্রয়োজন নেই। তুমি পাপী, অন্যায়কারী। যাও, চলে যাও।‘
লোকটির কথা আমার মনে আঘাত করল। সে-ও আমার অন্যায়ের কথা জানে!
আমি আর রূপা এগোতে লাগলাম। একটু এগোতেই পায়ে কাঁটা ফুটতে শুরু করল। যন্ত্রণায় আঁতকে উঠলাম আমরা। দাঁতে দাঁত চেপে এগোতে লাগলাম। পা দিয়ে রক্ত ঝরছে অনবরত। রূপা বলে উঠল, ‘পারব না। আমি পারব না।’
‘পারতে হবে, রূপা। আমাদের পারতে হবে।’
আবার আমরা এগোনোর চেষ্টা করলাম। বারবার পড়ে যাচ্ছে রূপা। ওর শরীরের নানান জায়গায় কাঁটা ফুটে যাচ্ছে। এক পর্যায়ে রূপা পড়ে গিয়ে বলে উঠল, ‘আমি আর এগোতে পারব না। কিছুতেই না।’ যন্ত্রণায় কাঁদতে লাগল একটানা।
‘চলো, রূপা। আমাকে ধরো। চেষ্টা করো।’
‘না, না, তুমি যাও। তুমি চলে যাও। আমি যাব না।’
‘রূপা, ওঠো….’
রূপা জবাব দিল না। হয়তো ঘোরের মধ্যে চলে গেছে। আমি বেশ কিছুক্ষণ রূপাকে ওঠানোর চেষ্টা করলাম। এরপর একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিলাম। রূপাকে ফেলেই আমি এগোব। দ্রুত এগোনোর জন্য আমি দৌড়াতে লাগলাম। ব্যথায় আমার পা অসাড় হয়ে গেল। তবু থামলাম না। পড়ে গেলাম বারবার। কিন্তু পরক্ষণেই আবার এগোতে লাগলাম। কতক্ষণ পেরিয়েছে জানি না। হঠাৎ তীব্র আলোর রেখা দেখতে পেলাম আমি। আমার চোখ ধাঁধিয়ে গেল। আলোর দিকে আরও দ্রুত দৌড়াতে লাগলাম। নিঃশ্বাস দ্রুত থেকে দ্রুততর হলো। মনে হচ্ছে বুকের উপর পাথর চাপা দেয়া। পেটের ভিতরের সবকিছু মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। তবু আমি এগিয়ে চললাম। সবকিছু হঠাৎই অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি আবার তীব্র অন্ধকারে ডুবে গেলাম। তীব্র…তীব্র অন্ধকার।
.
মোবাইলটা বাজছে। আমি চোখ মেলে তাকালাম। শরীরের কোথাও ব্যথা অনুভূত হচ্ছে না। মুখের মধ্যে দাঁতগুলো ঠিকমত আছে। হাত-পায়েও কোনও ক্ষত নেই।
আমি ফোন ধরলাম। মায়ের ফোন। মা উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, ‘কী রে, কী অবস্থা তোর? গতকাল থেকে তোকে ফোন করছি। ফোন ধরিস না কেন?’
আমার মনে পড়ে গেল। মা-বাবা নড়াইলে গেছেন। আমি বাসায় একা। মোবাইলের দিকে ভাল করে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। মোবাইলে তারিখ দেখাচ্ছে ৮ এপ্রিল। রাত নয়টা। আমি গতকাল রাত দশটায় ঘুমিয়ে পড়েছি। তার মানে আমার জীবন থেকে তেইশ ঘণ্টা হারিয়ে গেছে। আচ্ছা, রূপা কী করছে এখন? আমি আসলে খুব স্বার্থপর। মেয়েটাকে একা-একা ওই অন্ধকার জগতে রেখে এসেছি। সে হয়তো চিরতরে আটকা পড়ে গেছে ওখানে। খুব কষ্ট হতে লাগল আমার। ডুকরে কেঁদে উঠলাম।
আমি গ্যারাজ থেকে আমাদের গাড়িটা বের করলাম। যদিও বের করতে একটু ভয়-ভয় করছে। কারণ, কয়েকদিন আগেই এই গাড়িতে আমার একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমি সেটা মনে করতে চাই না। সব দুঃস্বপ্ন আমি ভুলে যেতে চাই।
একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে প্রিয় নান আর মুরগির গ্রিল খেয়ে নিলাম। রাতে বাসায় ফিরে আর ঘুমানোর সাহস করলাম না। পরদিন সকালে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করে তুমুল আড্ডায় মেতে উঠলাম। যা দেখছি তা-ই ভাল লাগছে। তবে মনের ভিতর কোথায় যেন একটা ভয়। অস্বস্তি দানা বাঁধছে। রাতেও আমার ঘুমাতে খুব ভয় লাগছিল। যদি আবার ওই জগতে ফিরে যাই? কিন্তু একসময় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখতে থাকলাম। স্বপ্নে রূপা আর আমি নৌকায় করে কোথায় যেন যাচ্ছি। আমার কোলে একটা ছোট বাচ্চা। রূপা বলল, ‘অ্যাই, নদীতে খুব স্রোত। বাবুকে সাবধানে রেখো।’
‘আচ্ছা।’
রূপা আবার বলল, ‘না, না। তুমি ওকে ফেলে দেবে। ওকে আমার কাছে দাও।’
রূপা আমার দিকে এগিয়ে এল। প্রচণ্ড স্রোতে নৌকাটা দুলছে। হঠাৎ তাল সামলাতে না পেরে নদীর মধ্যে পড়ে গেল রূপা। কিছুক্ষণ ভেসে থাকার পর ডুবে গেল।
আমার ঘুম ভেঙে গেল। ভয়ের অনুভূতি গ্রাস করল আমাকে। একটু পরে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।
সকালে ঘুম থেকে উঠে আনমনে পত্রিকাটা হাতে নিলাম। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব সংবাদ পড়তে লাগলাম। হঠাৎ শেষ পৃষ্ঠায় ছোট একটা নিউজে আমার চোখ আটকে গেল।
নিউজটার শিরোনাম: ‘৭২ ঘণ্টা কোমায় থেকে মৃত্যুবরণ করলেন রূপা।’ ভিতরে লেখা: ‘সড়ক দুর্ঘটনায় মারাত্মক আহত রূপা মৃত্যুবরণ করেছেন। গতকাল সন্ধ্যায় চিকিৎসকরা তাঁর মৃত্যুসংবাদ নিশ্চিত করেন। উল্লেখ্য, গত ৫ এপ্রিল উত্তরার রাজলক্ষ্মীতে প্রাইভেট কারের ধাক্কায় মারাত্মকভাবে আহত হন মেধাবী এ ছাত্রী। এ ব্যাপারে থানায় অপমৃত্যু মামলা দায়ের হয়েছে।’
আমার হাত থেকে পত্রিকাটি পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল আমার সেই অন্যায়টির কথা। গত ৫ এপ্রিল আমি এলোপাথাড়ি গাড়ি চালাচ্ছিলাম। উত্তরার রাজলক্ষ্মীতে এসে আমার গাড়ি একটা মেয়েকে ধাক্কা দেয়। আমি প্রাণভয়ে গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দ্রুত সরে পড়ি। ওই মেয়েটিই যে রূপা ছিল তা এখন বুঝতে পারছি।
রূপার প্রতি আমি দু’বার অন্যায় করেছি। একবার এই জগতে। একবার ওই অন্ধকার জগতে। এই অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত আমাকেই করতে হবে।
.
অনেক রাত। আমি মনেপ্রাণে সেই অন্ধকার জগতে প্রবেশ করতে চাইছি। একাগ্রচিত্তে ওখানে যাওয়ার চেষ্টা করছি আমি। পথনির্দেশক বৃদ্ধ বলেছিলেন, ‘যারা অন্ধকার জগৎ থেকে বাস্তব জগতে ফিরে যায়, তারা আবার চেষ্টা করলে অন্ধকার জগতে ফিরে আসতে পারে।
আমি সেই চেষ্টাই করছি। আমি ওই জগতেই স্থায়ীভাবে থাকতে চাই। এ-ও জানি, বাহাত্তর ঘণ্টা পেরোলেই বাস্তব জগতে মৃত্যু ঘটবে আমার। ভাবতে-ভাবতে চোখে এল রাজ্যের ঘুম।
আমি চোখ মেলে তাকালাম। আবার সেই তীব্র অন্ধকার। আমি তা হলে আবার সেই জগতে ফিরে এসেছি। তীব্র অন্ধকারেই আমি উঠে দাঁড়ালাম। রূপাকে খুঁজে বের করতে হবে। আমি ওর সঙ্গে চিরকাল থাকতে এ জগতে এসেছি। বলে উঠলাম, ‘রূপা…কোথায় তুমি?’
কেউ জবাব দিল না।
আমি আকুল হয়ে ডাকতেই লাগলাম, ‘রূপা…রূপা…’
টিক-টিক-টিক
এক
কলেজ কমপাউণ্ডে জারুল গাছটার নীচে বসে আছে ইলিয়াস। কেমন অস্থির দেখাচ্ছে তাকে। ইলিয়াসের খুব কাছের বন্ধু রুদ্র। ইলিয়াসের মন খারাপ দেখলে তার নিজের মনটাও উদাস হয়ে যায়।
‘মনটা খারাপ কেন, ইলিয়াস?’ রুদ্র জিজ্ঞেস করল।
‘কয়েকদিন ধরে বাসায় একা আছি। তাই ভাল লাগছে না,’ রুদ্রর দিকে না তাকিয়েই বলল ইলিয়াস।
‘একা কেন? তোরা না যৌথ পরিবার? আর সবাই কোথায়?’ বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল রুদ্র।
‘সবাই গ্রামে গেছে।’
‘তুই গেলি না কেন?’
‘সামনে টেস্ট পরীক্ষা। এ অবস্থায় কীভাবে যাব?’ ইলিয়াসের গলায় সামান্য ক্ষোভের প্রকাশ।
‘খাওয়া-দাওয়া কীভাবে করছিস?’
‘বুয়া আছে। সে সকালে এসে রান্না করে দিয়ে যায়।’
‘হঠাৎ পুরো পরিবার গ্রামে গেল?’
‘গ্রামে জমি-জমা নিয়ে একটু সমস্যা হয়েছে।’
‘তোদের বাসা তো কল্যাণপুরে, না?’
‘নাহ, এখন মালিবাগে থাকি। আমাদের এক জায়গায় বেশিদিন থাকতে ভাল লাগে না,’ ইলিয়াসের গলায় রহস্যের সুর।
‘তোরা পারিসও। প্রায় ষোলোজন মানুষ পরিবারে। এত মালপত্র নিয়ে বাসা বদলানো কি চাট্টিখানি কথা!’ একটু বিরতি দিয়ে রুদ্র বলল, ‘গত বছর কল্যাণপুরে তোদের বাসায় গিয়েছিলাম। মনে আছে?’
‘হ্যাঁ, মনে আছে। গিয়ে তো বসলিই না।’
‘হ্যাঁ, একটা জরুরি নোট আনতে গিয়েছিলাম।’
‘আজকে আমাদের বাসায় চল না। বাসায় কেউ নেই। রাতে ইচ্ছামত আড্ডা দেয়া যাবে,’ করুণ গলায় বলল ইলিয়াস।
রুদ্র একটু ইতস্তত করতে লাগল। রাতে বাসার বাইরে থাকাটা মা-বাবা ঠিক পছন্দ করেন না।
রুদ্র মাথা চুলকে বলল, ‘ইয়ে, দোস্ত, আসলে…’
ইলিয়াস হাত জোড় করে বলল, ‘প্লিজ। না বলিস না। আমার মনটা ভাল নেই।’
‘আচ্ছা, ঠিক আছে। আজ রাতে তোর সাথে থাকব। তবে বাসায় মিথ্যা বলতে হবে।’
‘কী বলবি বাসায়?’
‘বলব, গ্রুপ স্টাডি করার জন্য কলেজ হোস্টেলে থাকব।’
‘হুম, সেটাই ভাল। আমার বাসায় থাকবি, এটা বলার দরকার নেই। না হলে তোর মা-বাবা ভেবে বসবেন ইলিয়াসের সাথে মিশে তাঁদের ছেলেটা নষ্ট হয়ে গেছে।
ইলিয়াসের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যাক, আজ খুব ভাল একটা আড্ডা হবে।
দুই
মালিবাগের একটা ঘুপচির ভিতর ইলিয়াসদের বাসা। ইলিয়াস না থাকলে রুদ্র চিনে এই বাসায় আসতে পারত বলে মনে হয় না। দোতলা একটা পুরানো বাড়ি। বাড়িওয়ালা এখানে থাকেন না। ইলিয়াসরা কম ভাড়ায় পুরো বাড়িটাই ভাড়া নিয়েছে
রুদ্র চিন্তিত গলায় বলল, ‘দোস্ত, তোদের এই বাসায় তো ভূতের সিনেমার শুটিং করা যাবে। আমার তো বিকেল বেলাতেই কেমন গা ছমছম করছে।’
ইলিয়াস হেসে বলল, ‘আজ রাতে দুই বন্ধু মিলে ভূতের গল্প করব। ভাল মজা হবে।’
‘না, না। আমার হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে।’
‘আচ্ছা, ঠিক আছে। অন্য গল্প হবে,’ ইলিয়াস হেসে বলল।
বাড়ির ভিতর ঢুকতেই রুদ্র মৃদু স্বরে চিৎকার করে উঠল।
‘কী হয়েছে?’ চিন্তিত গলায় বলল ইলিয়াস।
‘গায়ে দুইটা টিকটিকি বসেছিল।’
‘হা! হা! টিকটিকি দেখে এত ভয় পেলি!’ বিদ্রূপের হাসি হাসল ইলিয়াস।
‘এত বড় টিকটিকি আমি জীবনেও দেখিনি।’
‘আমাদের বাসার টিকটিকিগুলো অনেক বড় সাইজের।’
‘তোদের কল্যাণপুরের বাসায়ও অনেক টিকটিকি দেখেছিলাম। তোরা টিকটিকি পুষিস নাকি?’ এবার রুদ্রর মুখে হাসি ফুটল।
‘আরে, টিকটিকি সব বাসায়ই আছে। খুঁজে দেখ, তোদের বাসায়ও টিকটিকি আছে।’
ওরা দু’জনে দোতলায় চলে গেল। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। দুপুরে ভাত খাওয়া হয়নি ওদের। ইলিয়াস ফ্রিজ থেকে নানা ধরনের খাবার বের করল। গোগ্রাসে খাওয়া শেষ করল ওরা। খাওয়া শেষে ইলিয়াস একটা হলুদ জুস খেতে দিল রুদ্রকে। রুদ্র গন্ধ শুঁকে বলল, ‘এটা কীসের জুস?’
‘আরে, খেয়েই দেখ না, বিষ তো আর না!’
রুদ্র জুসে চুমুক দিল। কেমন অদ্ভুত টক-মিষ্টি স্বাদ। তবে খেতে অসাধারণ। রুদ্র বলল, ‘কী দিয়ে বানানো হয়েছে এটা?’
‘আমি ঠিক জানি না। আমার দাদির গোপন রেসিপি। আমাদের বাসায় কেউ বেড়াতে এলে দাদি অতিথিকে এই জুস খেতে দেন।’
‘ওহ। দারুণ খেতে।‘
গল্প তেমন জমে উঠছে না। রুদ্রর মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করছে। গত দু’রাত ঠিকমত ঘুম হয়নি। এটা একটা কারণ হতে পারে।
কোন বিশেষ কারণ ছাড়াই রুদ্র বারবার চমকে উঠছে। কেন জানি মনে হচ্ছে পুরো ঘর ভর্তি অসংখ্য মানুষ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কোন রূমেই কোন মানুষের অস্তিত্ব নেই। ইলিয়াস বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলছে। বোঝা যাচ্ছে রুদ্রকে পেয়ে সে খুব খুশি হয়েছে। কিন্তু রুদ্রর কিছু মাথায় ঢুকছে না। হঠাৎ ঘরের মধ্যে দড়াম করে কিছু একটা পড়ল।
রুদ্র চমকে উঠে বলল, ‘কীসের শব্দ হলো?’
ইলিয়াস বলল, ‘কই, আমি তো কোন শব্দ শুনতে পাইনি।’
‘না, না। আমি স্পষ্ট শুনেছি।’
‘আরে, বাদ দে। বিড়াল-টিড়াল হতে পারে।’
রুদ্রর কিছু ভাল লাগছে না। কেন জানি বাসায় চলে যেতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু এখন ইলিয়াসকে একা রেখে যাওয়াটা খারাপ দেখাবে। ইলিয়াস হয়তো বুঝতে পেরেছে রুদ্রর কিছু একটা ভাল লাগছে না। তাই সে বলল, ‘আচ্ছা। তোকে আমাদের ছবির অ্যালবাম দেখাই।’
রুদ্রর ছবি দেখতে তেমন ইচ্ছা করছিল না। তবু সে ইলিয়াসের সঙ্গে ছবি দেখতে লাগল। বেশিরভাগই ইলিয়াসদের পারিবারিক ছবি। হঠাৎ ভিতরের রুমে টেলিফোন বেজে উঠল। ইলিয়াসের তেমন ভাবান্তর হলো না। বেশ কয়েকটা রিং হওয়ার পর রুদ্র বলল, ‘টেলিফোন বাজছে তো!’
ইলিয়াস আনমনে বলে বসল, ‘বাজুক। অন্য কেউ ধরবে।’
‘অন্য কেউ ধরবে মানে? বাসায় তো আর কেউ নেই।’
ইলিয়াস যেন একটু থতমত খেয়ে গেল। বলল, ‘হ্যাঁ। তাই তো। মনে ছিল না। আচ্ছা, তুই ছবি দেখ। আমি আসছি।’
রুদ্রর কেমন যেন মনের ভিতর একটা খটকা লাগছে। কোন কারণ ছাড়াই বুকের মধ্যে কাঁপুনি দিচ্ছে।
হঠাৎ একটা ছবিতে চোখ আটকে গেল রুদ্রর। নিলয়ের ছবি। ওদের সঙ্গে পড়ত নিলয়। হঠাৎ করেই দুই মাস আগে ছেলেটা নিখোঁজ হয়। পুলিস অনেক চেষ্টা করেছে, কিন্তু নিলয়ের কোন খোঁজ বের করতে পারেনি। রুদ্র এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিলয়ের ছবিটা অ্যালবাম থেকে বের করল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে ইলিয়াসদের বাসায় তোলা হয়েছে ছবিটা। ছবির পিছনে কলম দিয়ে তারিখ লেখা রয়েছে, ২০ জুলাই। রুদ্রর মাথা এলোমেলো হয়ে গেল। ২১ জুলাই তারিখ থেকে নিলয়ের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। ওর মা-বাবা কলেজে এসে অনেক কান্নাকাটি করেছিলেন। তারিখটা রুদ্রর স্পষ্ট মনে আছে। কারণ, ২১ জুলাই ওর মা-বাবার বিবাহবার্ষিকী। রুদ্র নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরল। তার মানে নিখোঁজ হওয়ার আগের দিন নিলয় ইলিয়াসের বাসায় ছিল?
নীচতলায় অনেক মানুষের কথা শোনা যাচ্ছে। পাশের ঘরেও কেউ যেন বিচিত্র স্বরে কথা বলছে। রুদ্রর আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে ইচ্ছা করছে না।
এমন সময় ইলিয়াস ঘরে এসে ঢুকল। রুদ্র নিলয়ের ছবিটা বালিশের নীচে লুকিয়ে ফেলল।
রুদ্র স্বাভাবিক গলায় বলল, ‘ইলিয়াস, বাসা থেকে ফোন এসেছিল। আব্বার শরীরটা হঠাৎ খারাপ হয়েছে। আমাকে যেতে হবে।’
ইলিয়াস চিন্তিত গলায় বলল, ‘তাই নাকি! ঠিক আছে, তুই চলে যা।’
রুদ্র উঠে দাঁড়াল। হঠাৎ তার মাথাটা ঘুরে উঠল। পেটের মধ্যেও কেমন যেন পাক দিচ্ছে। ইলিয়াসের চোখের দৃষ্টি কেমন যেন ভয়ঙ্কর হয়ে গেছে। সে মুখে বাঁকা হাসি ঝুলিয়ে বলল, ‘তুই নিলয়ের ছবিটা দেখে ফেলেছিস, না?’
রুদ্র ভয়ে ভয়ে ইলিয়াসের দিকে তাকাল।
ইলিয়াস ঠাণ্ডা গলায় বলল, ‘আসগরেরও একটা ছবি আছে। দেখিসনি?’
রুদ্রর শরীর কেমন অবশ হয়ে গেল। আসগরও ওদের সঙ্গে পড়ত। পাঁচ-ছয় মাস আগে সে-ও নিখোঁজ হয়।
ইলিয়াস বলল, ‘চল, তোকে বড় রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।’
রুদ্র হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে গেল।
ইলিয়াস জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে বলল, ‘দাদি কী সব জুস যে বানায়, সবার শুধু মাথা ঘোরে। দাদি, ভাল জুস বানাতে পারো না?’
হঠাৎ এক বৃদ্ধা মহিলার কণ্ঠ শুনতে পেল রুদ্র। জড়ানো কণ্ঠস্বর, শুনলেই গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ‘ঠিক আছে। এখন থেকে ভাল করে জুস বানাব। ভয়ঙ্করভাবে হেসে উঠলেন বৃদ্ধা। ইলিয়াস হাসিতে যোগ দিল। রুদ্র আরও বেশ কয়েকজনের হাসির শব্দ শুনতে পেল। সে জেগে থাকার অনেক চেষ্টা করছে। কিন্তু ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে এল।
তিন
কেউ একজন অনেক দূর থেকে রুদ্রকে ডাকছে। ও চোখ মেলে তাকাল। আলোতে পরিপূর্ণ একটা ঘর। রুদ্রর পুরো শরীর নগ্ন। হাত-পা শক্ত দড়ি দিয়ে বাঁধা। মুখে টেপ লাগানো। ওর সামনে উদ্বিগ্ন মুখে ইলিয়াস বসে আছে।
ইলিয়াস বলল, ‘দাদির জুসের প্রভাব চার-পাঁচ ঘণ্টা থাকে। এরপর ঘুম ভেঙে যায়। এখন কেমন লাগছে?’
রুদ্র নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করল। কিন্তু দড়িগুলো এতটুকু আলগা হলো না।
ইলিয়াস উপরের দিকে হাত তুলে জোরে বলল, ‘অনেক খিদে আমাদের। ক্ষুধার্তদেরকে তাদের কাজ করতে দে। নড়াচড়া করিস না।’
রুদ্র দেখতে পেল পনেরো-ষোলোটা টিকটিকি দেয়াল বেয়ে তার শরীরে বসেছে। ধীরে-ধীরে ওগুলোর আকার বহুগুণে বেড়ে গেল। রুদ্র ইলিয়াসকে আর দেখতে পেল না। সে-ও বড়সড় একটা টিকটিকি হয়ে গেছে। রুদ্র ছোট একটা বাচ্চার কণ্ঠ শুনতে পেল। ‘বাবা, চোখটা আমি খাই?’
‘খাও। আরাম করে খাও, বাবা।
বাচ্চা টিকটিকিটা আরাম করে রুদ্রর চোখ খেতে লাগল। চোখ হারানোর পরেও রুদ্র ভাসা-ভাসা অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছে। সে দেখতে পেল টিকটিকিগুলো তার সমস্ত শরীর খুবলে খুবলে খাচ্ছে। তার কেন জানি মনে হতে লাগল এটা একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়। একটু পরেই সে ঘুম থেকে জেগে উঠবে। দেখবে সে তার ঘরের খাটে শুয়ে আছে। সকালের রোদ তার পায়ে এসে পড়েছে।
রুদ্রর এই ভাবনায় ছেদ পড়ল। একটা টিকটিকি জোরে ডেকে উঠল, ‘টিক-টিক-টিক।’
দরজার ওপাশে
এক
সেলিম চাচাদের বাসায় দিপু খুব একটা যেতে চায় না। এর পিছনে মূল কারণটা একটু জটিল। সহজ করে বলা যায়, সেলিম চাচার মেয়ে নিরুপমার প্রতি ওর প্রচণ্ড দুর্বলতা রয়েছে। প্রেমে পড়লে মানুষের আচার-আচরণ চোরের মত হয়ে যায়। ওর অবস্থাও সেরকম। শুধু মনে হয়, বারবার সেলিম চাচাদের বাসায় গেলে সবাই আসল ঘটনা বুঝে ফেলবে। তবে ওদের মধ্যে কোনও সম্পর্ক গড়ে উঠলে আশা করা যায় দুই পরিবারের কেউই কোনও আপত্তি করবে না। কিন্তু দিপুর মূল দুশ্চিন্তাটা নিরুপমাকে নিয়ে। ছোটবেলা থেকেই নিরুপমার সঙ্গে ওর বন্ধুত্বের সম্পর্ক রয়েছে। এখন প্রিয় বন্ধুকে কি নিরুপমা ভালবাসতে পারবে?
স্কুল-কলেজে পড়ার সময়ে নিরুপমার প্রতি বিশেষ কোনও দুর্বলতা অনুভব করেনি। কিন্তু যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে সেকেণ্ড ইয়ারে উঠল, তখন কীভাবে যেন সব ওলট-পালট হয়ে গেল। সেদিনটার কথা খুব মনে পড়ে, যেদিন নিরুপমাকে প্রথম শাড়ি পরতে দেখেছিল, নীল রঙের জামদানি শাড়ি। একটা নীল রঙের টিপও ছিল কপালে। ব্যস, এটুকুই, আর কোনও সাজসজ্জা ছিল না। তাতেই মনে হচ্ছিল দিপুর সামনে একটা নীল পরী বসে আছে, যার দিকে শুধু তাকিয়ে থাকতে হয়। সেদিন প্রথমবারের মত নিরুপমার সঙ্গে কথা বলতে লজ্জা পাচ্ছিল ও। ওর চোখের দিকেও তাকাতে পারছিল না, মনে হচ্ছিল হুট করেই ও অনেক বড় একটা অপরাধ করে ফেলেছে।
অনার্স শেষ করেই একটা ব্যাংকে চাকরি শুরু করেছে দিপু। এত দ্রুত চাকরি শুরুর কারণ হচ্ছে, নিরুপমাকে মনের সব কথা খুব দ্রুত খুলে বলতে চায়। তারপর আপন করে পেতে চায়।
সেলিম চাচা দিপুর আপন চাচা নন। দিপুর বাবার মামাতো ভাই। কিন্তু তাঁদের সম্পর্ক আপন ভাইয়ের চেয়েও বেশি গভীর। দিপুর জীবনের একটা বড় অংশ সেলিম চাচা আর নিগার চাচীর ভালবাসায় পরিপূর্ণ হয়েছে। চাচা সারাজীবন প্রথম শ্রেণীর সরকারি চাকরি করেছেন, কিন্তু জীবনে কখনও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেননি। তাই ঢাকা শহরে নিজের বাড়ি করা হয়নি। এখনও তাঁকে ভাড়া বাসায় বসবাস করতে হয়। সাভারে অবশ্য তিন কাঠা জমি কিনেছেন, তবে কবে বাড়ি বানানোর সুযোগ হবে, এখনও জানেন না।
দুই
সেলিম চাচারা নতুন বাসায় উঠেছেন। আগের বাসাটার সবকিছু ভাল ছিল, কিন্তু পানি ঠিকমত পাওয়া যেত না। অগত্যা নতুন বাসা খুঁজতে হলো। নতুন বাসাটা পাঁচতলা, তিনতলায় থাকবেন সেলিম চাচা। নতুন বাসাটা আগের বাসার থেকে অনেক সুন্দর। সম্প্রতি বাড়িতে নতুন রং করা হয়েছে এবং সব রুমে নতুন টাইলস দেয়া হয়েছে। তিনতলাটা দীর্ঘদিন ফাঁকা পড়ে ছিল। তাই বাড়িওয়ালা সবকিছু নতুন করে সংস্কার করেছেন। দিপু, ওর আব্বু, আম্মু চাচাদের বাড়ি বদলের সময় যথাসাধ্য সাহায্য করল। দিপুর নজর অবশ্য নিরুপমার দিকেই বেশি ছিল। কে জানে নিরুপমা হয়তো ওর দুর্বলতা কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছে। আজকাল প্রায়ই ফোনে কথা হয় ওদের। ফেসবুকে মেসেজও আদান- প্রদান হয় অনেক। দিপু মাঝে-মাঝে ইঙ্গিতে ওর ভাল লাগার কথা বোঝানোর চেষ্টা করে। নিরুপমা বুঝতে পারে কি না, কে জানে।
নতুন বাসায় সবকিছু দ্রুত গুছিয়ে নিলেন নিগার চাচী। তাঁর কর্মদক্ষতা নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। একাই একশো। দিপুর আম্মুও অবশ্য যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন।
সকালে অফিসের জন্য তৈরি হচ্ছে দিপু, সেই মুহূর্তে সেলিম চাচার ফোন। এত সকালে ওনার ফোন পেয়ে বেশ অবাকই হলো ও। সেলিম চাচা বললেন, ‘দিপু, আজ অফিস শেষ করে আমাদের বাসায় একটু আসতে পারবে?’
দিপু বলল, ‘হ্যাঁ, চাচা। অবশ্যই আসতে পারব।’
‘আচ্ছা, ঠিক আছে। চলে এসো।’
‘চাচা, কোনও সমস্যা?’
‘তেমন কিছু না। সামনাসামনি বলব।’ বলেই ফোনটা রেখে দিলেন। দিপু চিন্তায় পড়ল। সারাদিন অফিসে অস্বস্তিতে কাটাল। অফিস শেষ করে এক মুহূর্ত দেরি না করে সেলিম চাচাদের বাসার দিকে রওনা দিল
আজ সেলিম চাচাকে অনেক গম্ভীর মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে তাঁর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। দিপুর মনের ভিতর ভয়ের অনুভূতি দানা বাঁধছে। সে কি কোনও ভুল করেছে? দিপু প্রায় পনেরো মিনিট বসে আছে, এর মধ্যে সেলিম চাচা ওর সঙ্গে একটা কথাও বলেননি। তাঁর সামনে চায়ের কাপ, কিন্তু একবার চুমুকও দেননি। তিনি অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন, মনে হচ্ছে আনমনে কিছু ভাবছেন।
অন্যদিকে তাকিয়ে থেকেই সেলিম চাচা বললেন, ‘দিপু।’
‘জী, চাচা।’ হঠাৎ শব্দ শুনে কিছুটা চমকে উঠল দিপু।
‘তোমার সাথে কি নিরুপমার নিয়মিত কথা হয়?’
প্রশ্নটা দিপুর কাছে পরিষ্কার নয়। তাই আমতা-আমতা করল। বলল, ‘জী…মানে…’
কেন জানি গলা শুকিয়ে যাচ্ছে ওর। পানি খাওয়া দরকার। নিরুপমার সঙ্গে কথা বলা নিয়ে কি কোনও ঝামেলা হয়েছে? নিরুপমা কি ওর কোনও আচরণে রাগ করেছে? মাথার ভিতর রাজ্যের সব প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে।
চাচা আবার বললেন, ‘আমার যতদূর মনে হয়, নিরুপমা আর তুমি খুব ভাল বন্ধু। তাই তোমাকে ডেকেছি। আর তুমি তো এ বাড়িরই ছেলে।’
কথাটা শুনে দিপুর ভয়ের ভাবটা কিছুটা কাটল। ‘এ বাড়ির ছেলে’ কথাটা মধুর মত শোনাল।
সেলিম চাচা আবার বললেন, ‘নিরুপমাকে নিয়ে একটু ঝামেলায় পড়েছি। তোমার সাথে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাই।’
‘কী সমস্যা, চাচা?’
‘নিরুপমা যে রুমে থাকে, সেই রুমে একটা অ্যাটাচড বাথরুম রয়েছে। সেটাতে বিশাল বড় একটা তালা ছিল। বাড়িওয়ালা প্রথম দিনেই বলেছিলেন, ‘এই বাথরুমে কোনওক্রমেই ঢোকা যাবে না।’ নিরুপমা হেসে বলেছিল, ‘কেন, চাচা? ভূত আছে নাকি?’ বাড়িওয়ালা কথাটা ভালভাবে নেননি। রাগতস্বরে বলেছিলেন, ‘মা, এ নিয়ে আর কোনও কথা বলতে চাই না। খবরদার, এই বাথরুমে কাউকে ঢুকতে দেবে না।’ আমার মেয়েটা একটু জেদি ধরনের, জানো তো। ওর মধ্যে জেদ চেপে গেল। বাড়িওয়ালা চলে যাওয়ার পর সে চেঁচিয়ে বলল, ‘এইসব কুসংস্কারের জন্য দেশ এখনও পিছিয়ে আছে। আরে, ওয়াশরুম নিয়ে এত ভয়ের কী আছে? আমি এই তালা ভাঙব। নিজের রুমে ওয়াশরুম থাকতে অন্য রুমে যেতে পারব না।’ আমি বললাম, ‘মা, বাড়িওয়ালা যখন নিষেধ করেছেন, তখন থাক না। আরও দুইটা বাথরুম আছে তো।’ নিরুপমা বলল, ‘না, বাবা। আমি এই ওয়াশরুমই ইউজ করব।’ ও তালাটা ভেঙে ফেলল। ঝকঝকে-তকতকে একটা বাথরুম। দেখে মনেই হয় না যে দীর্ঘদিন কেউ এটা ব্যবহার করেনি। পরিষ্কার করার প্রয়োজন ছিল না, তবু বাথরুমটা আবার পরিষ্কার করল নিরুপমা। নতুন লাইটও লাগাল। কয়েকদিন পেরিয়ে গেল। আমি বিষয়টা এত বেশি গুরুত্ব দিইনি। গত পরশু রাতে নিরুপমা বাথরুমে যাওয়ার পর ভয়াবহ কিছু কাণ্ড ঘটেছে।’
দিপু আঁতকে উঠে বলল, ‘কী হয়েছে, চাচা?’
‘কী ঘটেছিল নিরুপমা আমাদের সব বলেছে। তবে আমি চাই তুমি আবার ওর মুখ থেকে সব শোনো। পারলে আমার মেয়েটাকে একটু স্বাভাবিক করার চেষ্টা করো, বাবা। যাও, নিরুপমা রুমেই আছে।’
নিরুপমা তার রুমে শুয়ে ছিল। দিপু দরজায় নক করল। অনুমতি চাইল, ‘আসব?’
নিরুপমা বলল, ‘এসো, দিপু।’
দিপু ওর বিছানার পাশের চেয়ারে বসল। হাসিমুখে বলল, ‘কেমন আছ? অসুস্থ নাকি?’
‘হ্যাঁ। আমি অসুস্থ।’ নিরুপমার চোখ-মুখ লাল হয়ে আছে। জবুথুবু হয়ে একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে শুয়ে আছে। দেখে মনে হচ্ছে শীত লাগছে তার।
দিপু কৌতুকের সুরে বলল, ‘চাচা বললেন, তুমি নাকি বাথরুমে গিয়ে ভয় পেয়েছ?’
‘তুমি মজা পাচ্ছ?’ আহত গলায় নিরুপমার প্রশ্ন।
দিপু যেন সংবিৎ ফিরে পেল। মাথাটা এদিক-ওদিক নাড়িয়ে বলল, ‘না। না। আমি মজা করে কিছু বলিনি। আসলে পরিস্থিতিটা হালকা করার জন্য এমন সুরে কথা বলছিলাম। সরি।’
নিরুপমা চোখ বন্ধ করল। মনে হলো, তাকিয়ে থাকতে তার কষ্ট হচ্ছে। দিপুর নজর গেল বাথরুমটার দিকে। সেটার দরজায় একটা নতুন তালা ঝুলছে।
দিপু নিচু গলায় বলল, ‘আমাকে সবকিছু বলবে, প্লিজ?’
নিরুপমা চাদরটা ভালভাবে শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে বলল, ‘বলব। তোমাকে যে সব বলতেই হবে।’
‘হ্যাঁ, বলো।’
‘সেদিন ওয়াশরুমে ঢোকার পর কেমন যেন অস্বস্তি হচ্ছিল, অনুভব করছিলাম কিছু একটা ঠিক নেই। বেসিনের আয়নার দিকে বারবার চোখ চলে যাচ্ছিল। অজানা ভয় তখন আমাকে জেঁকে ধরেছিল, মনে হচ্ছিল আয়নার দিকে তাকিয়ে অন্য কারও মুখ দেখতে পাব। নাহ, তেমন কিছু ঘটেনি। আয়নার মধ্যে আমার মুখই দেখেছিলাম। এরপর শাওয়ার চালু করেছিলাম। সারাদিন অনেক পরিশ্রম করেছিলাম। তাই ঠাণ্ডা পানিতে শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছিল। কিছু সময় পার হওয়ার পর, আমার অস্বস্তিটা বাড়ল। মনে হলো, কেউ আমার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। চমকে পিছনে তাকালাম, কিন্তু পিছনে কেউ ছিল না। শাওয়ারের দিকে নজর গেল আমার। পানির বেগ ঠিকই ছিল। কিন্তু…’
‘কিন্তু কী?’
‘পানি অসম্ভব ময়লা ছিল। নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, পানির সাথে সাদা-সাদা ছোট টুকরো চলে এসেছে, চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সাদা টুকরোগুলো হাতে নিয়ে বুঝলাম, ওগুলো…’ নিরুপমা চোখ ঢেকে ফেলল।
‘ওগুলো কী ছিল?’
‘আমি বলতে পারব না। ওহ…আমি বলতে পারব না।’
‘প্লিজ, নিরুপমা, বলো।’
‘ওগুলো…ওগুলো…মাংসের টুকরো ছিল।’
‘ওহ, মাই গড। কী বলছ এসব?’
‘হ্যাঁ। আমার পুরো শরীর যেন ঘিনঘিন করে উঠল। মনে হলো পালিয়ে আসি সেখান থেকে। সেই মুহূর্তে হঠাৎ পানির রং বদলে গেল। পানি ক্রমেই লাল হয়ে উঠল। বুঝতে পারলাম ওগুলো পানি নয়, রক্ত। এতক্ষণ কি তা হলে রক্ত আর মাংস দিয়ে গোসল করেছি? শাওয়ার বন্ধ করলাম আমি। কিন্তু কোনও লাভ হলো না। আগের মতই চলতে লাগল। এমন সময় মনে হলো কমোডের মধ্য থেকে কেউ শব্দ করছে। প্রথমে মৃদুস্বরে, এরপর শব্দের গতি ক্রমেই তীব্র হলো। আমি ধীরে-ধীরে কমোডের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম। কাঁপা হাতে কমোডের ঢাকনা তুলেছিলাম। এরপর নিজেকে ঠিক রাখতে না পেরে ভয়ে আর্তচিৎকার দিয়েছিলাম।’ হু-হু করে কেঁদে উঠল নিরুপমা।
‘নিরুপমা, কেঁদো না। শক্ত হও। সবকিছু বলো আমাকে। কমোডের ঢাকনা উঠিয়ে কী দেখতে পেয়েছিলে?’
‘আমি দেখলাম কমোডের মধ্যে একটা কাটা হাত। কিন্তু হাতে একটাও আঙুল নেই। আমি আর দেরি করিনি। দৌড়ে দরজার কাছে চলে গিয়েছি। প্রবল শক্তিতে দরজা খোলার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু আতঙ্কের সাথে লক্ষ করলাম, দরজা খুলতে পারছি না। মনে হচ্ছিল দ্রজা জ্যাম হয়ে গেছে। এমন সময় একটা গোঙানির আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম। তখন বিকালের আলো ভেন্টিলেটার দিয়ে পুরো ওয়াশরুমে ঢুকছিল। হঠাৎ আলোর পথে যেন এক রাশ অন্ধকার বাধা হয়ে এল। পুরো ওয়াশরুম ক্রমেই অন্ধকার হতে লাগল। পরিবেশটাও আশ্চর্য নীরব হয়ে উঠেছিল। শাওয়ারও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গোঙানির শব্দটা আবার শুনতে পেয়েছিলাম। আমি কাঁপতে-কাঁপতে বললাম, ‘কে-কে?’ কেউ একজন মুখ দিয়ে বিচিত্র শব্দ করল। আমি শব্দের উৎস খোঁজার জন্য এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলাম। কেন জানি মনে হচ্ছিল, ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে চলেছে। হঠাৎ ওয়াশরুমের উপরের দিকে নজর গেল আমার। উপরের দৃশ্য দেখে আমি যেন পাথরের মত জমে গিয়েছিলাম।’
‘কী ছিল সেখানে?’ প্রশ্ন করল দিপু।
একজন, মানে একটা মেয়ে সেখানে ঝুলছিল। অনেকটা বাদুড়ের মত। তার একটা হাত নেই। বুঝতে পারলাম এই মেয়েটাই এতক্ষণ শব্দ করছিল। আমি চিৎকার করে উঠলাম। মাথা ঘুরে পড়ে যেতে-যেতে দেয়াল ধরে নিজেকে সামলে নিয়েছিলাম। মেয়েটি দেয়াল থেকে নীচে নেমে এল। এমন বিশ্রী চেহারার মানুষ আমি আগে কখনও দেখিনি। চোখের মণি সাদা রঙের, মাথায় একটাও চুল নেই, আর কালো জিভটা ক্রমাগত নড়াচড়া করছিল। আমি এক-এক পা করে পিছনে সরে যাচ্ছিলাম, মেয়েটি কিছু না বলে আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। ভয়ে আমি কাঁদতেও ভুলে গিয়েছিলাম। তার চোখের দৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল আমাকে যে-কোনও সময় মেরে ফেলবে। হঠাৎ মেয়েটা আমাকে জাপটে ধরল। আমি নিজেকে ছাড়ানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা করছিলাম, কিন্তু সে এক চুলও সরেনি। আমার পিঠে সে তার ধারাল দাঁত দিয়ে কামড় বসিয়ে দিল। মুহূর্তেই পুরো পৃথিবী আমার সামনে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। অঝোরে রক্ত ঝরছিল বেশ বুঝতে পেরেছিলাম। আমি চিৎকার করে বলছিলাম, ‘ছেড়ে দাও। আমাকে ছেড়ে দাও।’ আমার কথায় যেন ম্যাজিকের মত কাজ হয়েছিল। মেয়েটা আমাকে ছেড়ে দিল। এরপর কানের কাছে মুখ এনে কিছু কথা বলল। তারপর মেয়েটা কোথায় যেন হারিয়ে গেল। ওয়াশরুমে আবার আলো ফিরে এল। আমি দরজা আবার খোলার চেষ্টা করলাম। এবার দরজা খুলল। আমি বাইরে এসে বাবাকে ডাকলাম। এরপর আমার আর কিছু মনে নেই। সম্ভবত আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমার দূরসম্পর্কের খালাতো বোন ডাক্তার। সে এসে আমার পিঠের ক্ষতে ড্রেসিং করে দিয়েছিল। এরপর বাবা ওয়াশরুমে একটা বড় তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন।’
দিপু বলল, ‘সেই মেয়েটা তোমাকে কানে-কানে কী বলেছিল?’
‘না। না। আমি আর কিছু বলব না।’
নিরুপমা আর কিছু বলতে চাইল না। দিপু বুঝতে পারল এসব চিন্তা করতে কষ্ট হচ্ছে ওর। নিরুপমা আদুরে গলায় বলল, ‘তুমি আমার কাছে একটু আসবে?’ দিপু চেয়ার নিয়ে নিরুপমার বিছানার কাছে চলে গেল। নিরুপমা দিপুর হাতটা শক্ত করে ধরল। দিপুর পুরো শরীরটা ঝিমঝিম করে উঠল। নিরুপমা আগে কখনও ওর হাত ধরেনি। নিরুপমা বিড়বিড় করে বলল, ‘তোমাকে একটা কথা বলব, কিছু মনে করবে না তো?’
‘হ্যাঁ। বলো।’ দিপুর গলাটা কেমন যেন কেঁপে উঠল
কেন জানি আজই বলতে ইচ্ছা করছে। হয়তো এটা বলার উপযুক্ত সময় নয়। তবু আমি আজ বলব। দীর্ঘদিন ধরে মনের মধ্যে লালন করা কথাটা আজ বলব।’
‘বলো, কোনও সমস্যা নেই।’ দিপুর গলার কাছে কিছু একটা যেন আটকে গেছে।
‘আমি তোমাকে ভালবাসি। অনেক ভালবাসি
দিপুর মনে হলো সে ভুল শুনছে। যে কথাটা সে বহুদিন ধরে বলার চেষ্টা করছিল, সেটা নিরুপমা এত সহজে বলে দিল! দিপু স্বপ্ন দেখছে না তো? নিরুপমা এখনও ওর হাত শক্ত করে ধরে আছে। ধীরে-ধীরে বিছানায় উঠে বসল। এরপর বলল, ‘তুমি কি আমার পাশে থাকবে, দিপু?’
এত আবেগ, ভালবাসার জবাবে ওর কী বলা উচিত জানে না, এক শব্দে বলল, ‘থাকব।’
‘আমাকে ভালবাসো তো?’ অনুনয়ের সঙ্গে বলল নিরুপমা।
‘হ্যাঁ। ভালবাসি। ভালবাসি। ভালবাসি।’ আহা! কথাটা বলতে কতই না ভাল লাগছে দিপুর। মনে হচ্ছে ক্রমাগত ভালবাসি-ভালবাসি বলতেই থাকে।
এরপর হুট করেই নিরুপমা দিপুকে জড়িয়ে ধরল। হু-হু করে কেঁদে ফেলল। ‘আমাকে ফেলে যেয়ো না, দিপু। আমার সব বিপদে পাশে থেকো।’ দিপুও সুযোগটা হাতছাড়া করল না। নিরুপমাকে খুব শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রাখল। মনে হচ্ছিল সে এই পৃথিবীতে নেই। কেন জানি মনে হচ্ছে এটা কোনও স্বপ্নদৃশ্য।
তিন
নিরুপমা ফোন করে ওদের বাসায় যেতে বলল দিপুকে। আজ অন্য পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সব বাদ দিয়ে সেলিম চাচাদের বাসার দিকে রওনা দিল দিপু।
নিরুপমাকে আজ খুব খুশি-খুশি লাগছে। দিপুকে সরাসরি নিজের বেডরুমে নিয়ে গেল। সেলিম চাচা আর নিগার চাচী বিষয়টা নিয়ে কিছু মনে করবেন কি না, এই ভয় হচ্ছিল ওর। কিন্তু নিরুপমার মধ্যে কোনও ভ্রুক্ষেপ লক্ষ করল না। নিরুপমা ওখানেই থেমে থাকল না। রুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। দিপু লাফিয়ে উঠে বলল, ‘দরজা বন্ধ করছ কেন?’
‘হা-হা। ভয় পাচ্ছ কেন, বোকা ছেলে? একটু আরাম করে গল্প করতে চাই তোমার সাথে, এর বেশি কিছু না।’
‘চাচা-চাচী যদি কিছু মনে করেন?’
‘বাবা-মা কিছুই মনে করবেন না, আমি তাঁদের সব খুলে বলেছি।’
‘বলো কী? কী সর্বনাশ!’
‘সর্বনাশের কিছু নেই। আমি তাঁদের বলেছি দ্রুত আমাদের বিয়ের ব্যাপারে কথা বলতে। তাঁরাও সম্ভবত মনে-মনে এই স্বপ্নই দেখেছিলেন। তোমার বাবা- মা’র সাথে প্রাথমিক কথাও নাকি হয়ে গেছে।’
‘আম্মা-আব্বা তো আমাকে কিছু বলেননি!’ বিস্মিত গলায় বলল দিপু।
‘হয়তো কথা আর একটু এগোলে বলবেন।’
‘তুমি এত দ্রুত কীভাবে সব ম্যানেজ করলে?’
‘হা-হা। আমার কাছে জাদু আছে,’ রহস্যমাখা গলায় নিরুপমা বলল।
আজ দিপু নিজেই নিরুপমাকে আলিঙ্গন করল। নিরুপমা দিপুর গালে একটা চুমু এঁকে দিল। ওরা অনেক গল্প করল। ভবিষ্যৎ স্বপ্নের গল্প, ভালবাসার গল্প, গল্প যেন শেষই হয় না। নিরুপমা হঠাৎ লাজুক গলায় বলল, ‘তোমাকে একটা জিনিস দেখাতে ইচ্ছা করছে।’
‘কী?’
‘সেদিন মেয়েটা পিঠের যে জায়গাটায় কামড় দিয়েছিল, সেই জায়গাটা।’ দিপুর শরীরের ভিতর দিয়ে আলোড়ন বয়ে গেল। এত সৌভাগ্য কি ওর হবে? দিপু মাথা নাড়ল। ‘হ্যাঁ। আমি দেখতে চাই।’
‘নাও। জামার পিছন দিকের বোতাম দুটো খোলো,’ নিরুপমা মাথা নিচু করে বলল।
দিপু লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছিল। এগোনোর সাহস পাচ্ছিল না। নিরুপমা হেসে বলল, ‘থাক। এত লজ্জা পেতে হবে না। এই বিষয়টা আমাদের বাসর রাতের জন্য তোলা রইল।’
চার
সবকিছু ভালই চলছিল। দ্রুত একটা ঘরোয়া আয়োজনের মধ্য দিয়ে নিরুপমা আর দিপুর বিয়ে হবে। কিন্তু দুঃস্বপ্নের মত আবার বাথরুমের সেই ঘটনাগুলো সামনে চলে এল। এখনও সেই ঘটনার রেশ নিরুপমাকে টানতে হচ্ছে। আজ সেলিম চাচাদের বাসায় ও আসার পর থেকেই নিরুপমা আকুল হয়ে কাঁদছে। দিপুর অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে, কী যে বিপদে পড়েছে মেয়েটা। সেলিম চাচা নিরুপমার ঘরের ওয়াশরুমে একটা বড় তালা ঝুলিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি। বাথরুমের সেই মেয়েটা প্রায়ই নিরুপমার স্বপ্নে দেখা দিচ্ছে। বারবার বলছে যে খুব তাড়াতাড়ি নিরুপমার জীবন শেষ করে দেবে। খুব কষ্ট দিয়ে মারবে নিরুপমাকে। তার অনেক দিনের খিদে। নিরুপমাকে দিয়ে তার খিদে মেটাবে।
সেলিম চাচা বাড়ি বদলের চিন্তা করছেন, কিন্তু নিরুপমা বলেছে বাড়ি বদলে কোনও কাজ হবে না। বরং বাড়ি বদলানোর চেষ্টা করলে মেয়েটা তখনই তাকে মেরে ফেলবে।
দিপুর মনের মধ্যে কেমন যেন একটা ক্রোধের ভাব জেগে উঠল। নিরুপমাকে রক্ষা করতেই হবে। আগে এই বাসার বাথরুমের ইতিহাসটা জানা দরকার। দিপু সেলিম চাচার সঙ্গে কথা বলে বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা করতে গেল।
সেলিম চাচাদের বাড়িওয়ালা নবির শেখ বয়স্ক মানুষ। বয়স ষাট-পঁয়ষট্টি হবে। কথাবার্তা বলেন স্পষ্ট গলায়। তিনি দিপুকে দেখে কথা বলার তেমন কোনও আগ্রহ দেখালেন না। কেমন যেন সরু চোখে তাকিয়ে রইলেন। উঁচু গলায় বললেন, ‘আমি তো বাড়ি ভাড়া দেয়ার সময়েই বলেছিলাম ওই বাথরুমে কেউ ঢুকবেন না। আমার কথা শুনেছেন?’
দিপু চুপ করে রইল।
নবির শেখ আবার বললেন, ‘নিরুপমা মেয়েটা বেশি বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। সাহস খুব দরকারী একটা জিনিস। তবে মুরব্বীদের উপদেশ মেনে চলাও সমান দরকারী। ছোট ভুলের বড় শাস্তি পাবে মেয়েটা।’
দিপু জিজ্ঞেস করল, ‘কিন্তু কেন এমন হচ্ছে? এই বাথরুমের রহস্যটা কী?’
নবির শেখ উত্তর না দিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন। দিপু তাগাদা দিয়ে বলল, ‘আমাদের সবকিছু জানা প্রয়োজন। এর সাথে নিরুপমার জীবন-মরণ জড়িত।’
নবির শেখ দিপুর দিকে একটু ঝুঁকে বললেন, ‘আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে ওই বাথরুমে এলিনা নামে একটা মেয়ে মারা গিয়েছিল।’
‘কীভাবে মারা গিয়েছিল?’
‘তার স্বামী তাকে মেরে ফেলেছিল। শুধু মেরেই ক্ষান্ত হয়নি, সে মেয়েটার একটা হাতও কেটে ফেলেছিল। আর পুরো শরীরটা খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে বিকৃত করেছিল। পরে অবশ্য এলিনার স্বামীরও ফাঁসি হয়েছিল। তখন আমার বাবা বেঁচে ছিলেন। তিনি ওই বাথরুমটা তালাবদ্ধ করে রাখেন। তিনি দিব্যদৃষ্টির মাধ্যমে বুঝতে পেরেছিলেন, এই বাথরুমটা ব্যবহার করা নিরাপদ নয়। এখানে এলিনার আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাই কাউকে বাড়ি ভাড়া দেয়ার আগে বাবা বলতেন, কোনওক্রমেই বাথরুমটা খোলা যাবে না। কিন্তু নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি মানুষের আকর্ষণ খুব বেশি। তাই অনেক ভাড়াটিয়া আমাদের নিষেধ শোনেনি, তার ফলাফল হয়েছে ভয়াবহ। এ পর্যন্ত পাঁচজন ওই বাথরুমে মারা গেছে। প্রতিবারই থানা-পুলিশ হয়েছে। কিন্তু কাকে ধরবে পুলিশ, মৃত মানুষকে তো আর গ্রেফতার করা যায় না।’
‘যারা মারা গিয়েছিল তাদের মৃত্যু কীভাবে হয়েছিল কিছু জানা গিয়েছিল?’
‘প্রত্যেকেরই শরীরের খণ্ডাংশ পাওয়া গেছে। কেউ যেন তাদের খুবলে খুবলে খেয়েছে। কিছু হাড়, কিছু মাংস আর রক্ত এদিক-সেদিক পড়ে ছিল। এমন বীভৎস দৃশ্য-কী আর বলব, আমার মত শক্ত মনের মানুষ পর্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তাই গত সাত বছর আমি তিনতলাটা ভাড়া দিইনি। এবার একটু আর্থিক টানাটানির জন্য সেলিম সাহেবের কাছে বাসাটা ভাড়া দিয়েছিলাম। তাঁদের কঠিনভাবে নিষেধ করেছিলাম, কোনওক্রমেই যেন বাথরুমের দরজাটা খোলা না হয়। কিন্তু নিরুপমা মেয়েটা আমার কথা শোনেনি।’
নবির শেখ চিন্তিত গলায় আরও বললেন, ‘বিষয়টা খুবই রহস্যজনক। আজ পর্যন্ত কোনও মানুষ এলিনার কাছ থেকে জীবিত ফিরতে পারেনি। নিরুপমাই প্রথম যে প্রাণে বেঁচে গিয়েছে।’
‘হ্যাঁ। নিরুপমা ভাগ্যের জোরে প্রাণে বেঁচে গেছে, কিন্তু এখন এলিনা নামের মেয়েটা বলছে, নিরুপমাকে সে মেরে ফেলবে। এখন আমরা কী করতে পারি?’
‘বাসা ছেড়ে চলে যেতে পারেন। আর কোনও হুজুর ডেকে চেষ্টা করে দেখতে পারেন, নবির শেখ জবাব দিলেন।
‘কিন্তু এলিনা স্বপ্নে বলেছে, বাসা ছেড়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সেই মুহূর্তে নিরুপমাকে মেরে ফেলবে।’
‘এখন পর্যন্ত নিরুপমা বেঁচে আছে এটাই আশ্চর্যের।’ চশমাটা খুলে ফেললেন নবির শেখ।
‘আচ্ছা, যে পাঁচজন মারা গিয়েছিল তাদের কতজন নারী আর কতজন পুরুষ?’ দিপু জিজ্ঞেস করল।
নবির শেখের মুখটা আরও একটু গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি বললেন, ‘তাদের পাঁচজনই পুরুষ ছিল। পুরুষদের কৌতূহল মনে হয় একটু বেশিই থাকে।’
‘আচ্ছা, আপনি কখনও ওই বাথরুমে ঢুকেছিলেন?’
‘হ্যাঁ। প্রতিটা মৃত্যুর পর পুলিশের সাথে আমিও ঢুকেছিলাম। মৃতদেহগুলো বাথরুমেই পড়ে ছিল। তবে আমার চোখে বাথরুমের আলাদা কোনও বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েনি।’
‘আপনি বাথরুমটা স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেননি কেন?’
‘এটা ভুলই হয়েছিল। আসলে সাত বছর বাড়িটা ভাড়া দেয়া হয়নি, তাই ভেবেছিলাম ওই অশুভ জিনিসটার সম্মুখীন হয়তো আর হতে হবে না। কিন্তু…এবার বাথরুমটা স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেব।’
পাঁচ
এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে কি বিয়ের কথা চিন্তা করা যায়? কিন্তু দুই পরিবার ওদের বিয়ে ঠিক করল। দিপুর আম্মা-আব্বাও পুরো বিষয়টা জানতে পেরেছেন। তাঁরা মনে করছেন বিয়ের পর নিরুপমা শ্বশুরবাড়ি চলে গেলে সব ঝামেলা থেকে মুক্তি মিলবে। আনন্দের বিষয় হচ্ছে, বিয়ে ঠিক হওয়ার পর নিরুপমা এলিনাকে আর স্বপ্নেও দেখেনি।
দিপু এখন প্রায় প্রতিদিনই নিরুপমাদের বাসায় যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু দিপুকে দেখে নিরুপমা কেন জানি আগের মত খুশি হয় না। তার চোখের নীচে কালি পড়েছে, ব্রণে ভরে গেছে মুখ। আর মাথার চুলগুলো জট পাকিয়ে আছে। বোঝাই যাচ্ছে নিজের শরীরের প্রতি কোনও যত্ন নিচ্ছে না। দিপু নিরুপমার মাথায় হাত রেখে বলে, ‘এ কী অবস্থা তোমার?’
একদিন নিরুপমা কাতর গলায় বলল, ‘আমাকে তুমি মাফ করে দিয়ো।’,’অ্যাই, বোকা মেয়ে, মাফ চাইছ কেন? তুমি কী অপরাধ করেছ?’
নিরুপমা জোর করে হাসার চেষ্টা করল। বলল, ‘মাফ চাইতে ইচ্ছা হলো, তাই মাফ চাইলাম।’
দিপু বুঝতে পারল নিরুপমার মন থেকে ভয়টা এখনও দূর হয়নি। সান্ত্বনার ভঙ্গিতে বলল, ‘আমি তো কয়েকদিন পরেই সবসময় তোমার সাথে-সাথে থাকব, দেখি কে তোমার ক্ষতি করে।’
‘হুম।’ বোঝা যাচ্ছে দিপুর কথায় নিরুপমা তেমন ভরসা করতে পারেনি।
দিপু কথা ঘুরিয়ে বলল, ‘আমি কিন্তু বিয়ের রাতে তোমার পিঠের সেই ক্ষতটা দেখব, মনে আছে তো?’
নিরুপমা এবার হাসল। দিপু দুষ্টুমির হাসি হেসে বলল, ‘আর ওইদিন…’
‘ওইদিন কী?’
‘হা-হা। আরও অনেক কিছু করব।’
কেন জানি নিরুপমা আবার কাঁদতে লাগল। বেচারী বড্ড চিন্তায় আছে। দিপু এই মেয়েটাকে কিছুতেই আর কষ্ট পেতে দেবে না, কিছুতেই না।
ছয়
একটা ছোট ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিরুপমা আর দিপুর বিয়ে হলো। অল্প কিছু কাছের মানুষকে দাওয়াত দেয়া হলো। পরবর্তীতে দুই পরিবারের যৌথ উদ্যোগে একটা বড় অনুষ্ঠান করা হবে। বিয়ের রাত। দিপু নিরুপমাদের বাসায়ই থাকবে। পরদিন দুপুরের দিকে বউ নিয়ে বাড়ি ফিরবে।
বাসর রাতে দিপু আর নিরুপমা। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সারতে বেশ দেরি হয়েছে, দু’জনেই প্রচণ্ড ক্লান্ত। খুব ঘুম পাচ্ছে। কিন্তু বাসর রাতে সম্ভবত বোকারাই শুধু ঘুমায়। তাই জেগে রইল ওরা। বিয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নিরুপমা ক্রমাগত কেঁদেছে। এখন অবশ্য শান্তমুখে বসে আছে। তবে চেহারায় কেমন যেন তীব্র বেদনার ছাপও দেখা যাচ্ছে। বিয়ের সময়ে সব মেয়েরই মনে হয় এমন হয়।
দিপু বিছানায় বসতেই নিরুপমা বলল, ‘আমাকে মাফ করে দিয়ো, দিপু।
‘তোমার কী হয়েছে বলো তো। এত মাফ চাইছ কেন? তুমি মারা যাবে নাকি? যেভাবে মাফ চাইছ।’ দিপু জোরে হেসে উঠল।
‘আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। খুব কষ্ট। তুমি বুঝবে না,’ হতাশামাখা কণ্ঠ নিরুপমার।
দিপু নিরুপমাকে শক্ত করে ধরে রইল। আজ সারারাত ওকে দিপু ভালবাসবে, ওর সবটুকু কষ্ট নিজের করে নেবে। ও বলল, ‘পিঠের সেই ক্ষতটা দেখতে চাই। আজ আমি লজ্জা পাব না। ঠিক আছে?’
এমন সময় বাথরুমের দরজায় মৃদু শব্দ হলো। দিপু চমকে উঠে লাইট জ্বালল। আশ্চর্য ব্যাপার, বাথরুমের দরজায় তালা নেই। শুধু একটা ছিটকিনি দেয়া। দিপু নিরুপমার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তুমি আবার এই বাথরুমের তালা খুলেছ?’
মাথা নিচু করে বলল, ‘হ্যাঁ।’
‘খবরদার তুমি আর বাথরুমে ঢুকবে না কখনও।’
‘ঠিক আছে,’ নিরুপমা বলল। ‘তুমি একটু আমার সাথে এসো।’
‘কোথায়?’
নিরুপমা উঠে দাঁড়াল। বাথরুমের দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দিপু পিছু- পিছু গেল। নিরুপমা বাথরুমের ছিটকিনিটা খুলে ফেলল। দিপু আঁতকে উঠে বলল, ‘এ কী করছ? বাথরুমে ঢুকছ কেন?’ সে দৌড়ে গিয়ে নিরুপমার হাত চেপে ধরল।
ততক্ষণে দরজাটা পুরো খুলে ফেলেছে। ভিতরটা তীব্র অন্ধকার।
‘এদিকে এসো, দিপু!’ নিরুপমার কণ্ঠে আহ্বান।
‘নিরুপমা, তুমি কী করছ?’
‘আমার কাছে এসো।’ নিরুপমার গলায় কাতরতা।
দিপু নিরুপমার আরও কাছে গেল।
নিরুপমা বলল, ‘বাথরুমের ভিতরটা একটু দেখো!’
‘কী দেখব?’
‘তোমার দেখা প্রয়োজন।’
দিপুর সবকিছু এলোমেলো লাগছে। এসব কী করছে নিরুপমা?
দিপু বাথরুমের দরজা দিয়ে খানিকটা ভিতরে ঢুকল। সেই মুহূর্তে নিরুপমা দিপুকে সজোরে ধাক্কা দিল। দিপু তাল সামলাতে না পেরে ধপাস করে বাথরুমের মেঝেতে পড়ে গেল। নিরুপমা বাইরে থেকে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিল। অন্ধকার, ভয়ঙ্কর অন্ধকারে দিপু ক্রমশ তলিয়ে যেতে লাগল।
দিপু উঠে দাঁড়িয়ে পাগলের মত দরজা ধাক্কাতে শুরু করল। ‘নিরুপমা, নি- নিরুপমা। দরজা-দরজা খোলো।’
নিরুপমার কথা শুনতে পাচ্ছে দিপু। কাঁদতে-কাঁদতে নিরুপমা বলছে, ‘আমাকে মাফ করে দিয়ো, দিপু। আমি তোমার কোনও কথা শুনতে পাচ্ছি না। বাথরুমের ভিতরের শব্দ বাইরে থেকে শোনা যায় না।’
একটু থেমে আবার বলল, ‘এলিনা সেদিন আমাকে কী বলেছিল তোমাকে বলা হয়নি। এলিনা সেদিন আমাকে ছেড়ে দিয়েছিল। আর বলেছিল, সে কোনও পুরুষকে দিয়ে তার খিদে মেটাতে চায়। আমাকে ত্রিশ দিন সময় দিয়েছিল। এর মধ্যে আমার ভালবাসার মানুষটিকে ওকে দিতে হবে। নয়তো আমাকে বাঁচতে দেবে না। বাথরুম থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে আমাকে শেষ করবে। তার সব আক্রোশ পুরুষদের প্রতি। সাত বছর ধরে অপেক্ষায় আছে এলিনা। আমি ওর কথায় রাজি হয়েছিলাম। এরপর বাথরুম থেকে মুক্তি পেয়েছিলাম। আমার বুকটা কষ্টে ফেটে যাচ্ছিল। তবু নিজেকে বাঁচানোর জন্য কাজটা করতে হয়েছে আমাকে। আমি বাবাকে দ্রুত বিয়ের আয়োজন করতে বলি। অবশ্য তাঁকেও এই বিষয়টা খুলে বলা হয়নি। এদিকে এলিনা প্রায়ই আমার স্বপ্নে আসে। আমাকে সবকিছু বারবার মনে করিয়ে দেয়। এই কারণেই আমি আগেভাগে বারবার তোমার কাছে মাফ চেয়েছি। একটু পর তোমার খণ্ডিত লাশটা বাথরুমে খুঁজে পাওয়া যাবে। সবাই ভাববে তুমি বাথরুমে ঢুকেছিলে, তাই এই বিপত্তি ঘটেছে। এখানে আমার দোষের কথা কারও মাথায়ও আসবে না।’
দিপু আর কোনও শব্দ শুনতে পাচ্ছে না। সম্ভবত নিরুপমার আর কিছু বলার নেই। দিপু চিৎকার করছে, ‘বাঁচাও। কেউ আমাকে বাঁচাও।’
বাথরুমের মধ্যে একটা পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছে সে। কেউ পা টেনে-টেনে হাঁটছে। বুঝতে পারল এলিনা তার দিকে এগিয়ে আসছে। কাঁপা গলায় বলল দিপু, ‘আ-আ-আমাকে মেরো না।’
এলিনার গরম নিঃশ্বাস দিপুর শরীরে লাগছে।
ভাঙা গলায় এলিনা বলল, ‘খিদে লেগেছে। কতদিন পুরুষের মাংস খাইনি। অ-অ-অনেক দিন-ন-ন্।’
এলিনা দিপুকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। দিপু হাল ছেড়ে দিল। দিপু জানে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারবে না। মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করার চেয়ে ভয়ঙ্কর বোধহয় আর কিছু নেই।
দিপু নিরুপমার কণ্ঠ শুনতে পাচ্ছে। নিরুপমা বলছে, ‘বাবা, ও, বাবা, দিপু বাথরুমে ঢুকেছে, বাবা, আমি অনেক নিষেধ করেছিলাম, তবু ঢুকেছে।’
সেলিম চাচা বলছেন, ‘এ কী বলছিস? চিন্তা করিস না, মা। আমি দরজা ভাঙার ব্যবস্থা করছি।’
পুরো বাড়িতে শোরগোল পড়ে গেল। দরজা ভাঙার আয়োজন চলছে। এলিনা দিপুর বুকের উপর উঠে বসেছে। দিপু জানে, সেলিম চাচা বাথরুমের দরজা ভাঙার আগেই মেয়েটা তার খিদে মিটিয়ে ফেলবে।
সাধনা
সাধনা – ১
এক
বাবাকে বারান্দায় আসতে দেখে নুযহাত বলল, ‘বাবা, সুপ্রভাত।’
‘সুপ্রভাত, মা,’ মেয়ের দিকে তাকিয়ে স্মিত হেসে বললেন রফিক সাদি।
‘কখন উঠেছিস তুই?’
‘অনেক আগে, ভোরে।’
‘ভোরে ওঠা তো তোর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, ভাল।’
‘তুমিও আগে অনেক ভোরে উঠতে। আমাকে কতবার বলেছ, সকালের প্রথম আলো শরীরে মাখলে দূর হয় সব অমঙ্গল।’
‘ঘুম ভেঙে যায় আগেই। কিন্তু বিছানা থেকে আর উঠতে ইচ্ছা করে না।’
‘বাবা, আম্মু মারা যাওয়ার পর অনেক বদলে গেছ তুমি। স্ত্রী মারা গেলে এত কষ্ট পায় পুরুষমানুষ, তোমাকে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। ‘
‘তোর মাকে হারিয়ে আমার মধ্যে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তা কোনও কিছুতেই পূরণ হওয়ার নয়,’ দূরে তাকিয়ে বললেন রফিক সাদি। —কিছু কষ্ট কাউকে বোঝানো যায় না।’
‘কষ্ট কি আমি কম পেয়েছি, বাবা? কিন্তু জীবনের প্রয়োজনে মানুষকে স্বাভাবিক হতে হয়। প্রায়ই আড়াল থেকে দেখি, মায়ের ছবি বের করে তুমি কাঁদছ।’ নরম সুরে বলল নুযহাত, ‘তুমি অফিসে ঠিকমত যাও না। আগে টেনিস খেলতে যেতে, তা-ও ছেড়েছ। আগের মত তোমাকে বই পড়তেও দেখি না। সারাদিন মুখ গম্ভীর করে বসে থাকো।’
‘কিছু ভাল লাগে না রে,’ অপরাধীর মত বললেন রফিক সাদি। আমাকে আরও একটু সময় দে, দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে।’
‘কচু ঠিক হবে,’ বলল নুযহাত, ‘গত এক বছরে যখন ঠিক হয়নি, তখন হবেই না।’
‘আচ্ছা, ঠিক আছে, কাল থেকেই নিয়মিত অফিসে যাব।’
‘হুঁ, মনে থাকে যেন।’
‘তুই তো দিন-দিন আমার মায়ের মত হয়ে যাচ্ছিস। কোথায় তোকে সান্ত্বনা দেব, উল্টো তুই আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিস।’
‘বাবা, তোমার কালো মুখ দেখলে আমার কষ্ট হয়।’
‘আচ্ছা, মা। আর মুখ কালো করে রাখব না। শুধু হাসব।’
‘গুড বয়।’ বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল নুযহাত। ‘বাবা, তোমাকে কিছু বলতে চাই।’
‘অনুমতি নিচ্ছিস কেন? সরাসরি বলে ফেল।’
‘আমার বয়স গত ফেব্রুয়ারিতে ছাব্বিশ হয়েছে,’ নুযহাতের মাথা নিচু ‘হ্যাঁ। তা তো আমি জানিই।
‘সব বাবার উচিত সঠিক সময়ে সঠিক পাত্রের হাতে মেয়েকে পাত্রস্থ করা।’ বাবার দিকে তাকাতে লজ্জা লাগছে ওর।
রফিক সাদি কিছুক্ষণ মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর হো-হো করে হেসে উঠলেন। মেয়ের কান ধরে বললেন, ‘এমন কথা শিখেছিস কোথা থেকে?
‘বাবা, হেসো না। আমার লজ্জা লাগছে।’
‘আমি তো বেশ কিছুদিন ধরেই তোর বিয়ে নিয়ে ভাবছি। তোর কথায় আরও একটু জোর পেলাম। তোর কোনও পছন্দ আছে নাকি?’
‘হ্যাঁ, আছে।’
‘কী করে ছেলে? নাম কী?’
‘আমাদের সাথেই মাস্টার্সে পড়ছে। নাম জয়।’
‘ওহ্। চাকরি করছে না?’
‘বাবা, ওর আসলে চাকরি না করলেও চলবে। ওদের প্রচুর জায়গা-জমি। নানা ধরনের ব্যবসাও আছে।’
‘তবু ছেলে চাকরি না করলে, কেমন যেন দেখায় না ব্যাপারটা?’
‘চাকরি একসময় নিশ্চয় করবে। আপাতত ওর বাসা থেকে বিয়ে নিয়ে খুব তাগাদা দিচ্ছে।‘
‘ও, আচ্ছা, ঠিক আছে। ছেলেটাকে নিয়ে আয় একদিন।’
‘কালই আনি, বাবা?’
‘হ্যাঁ। দুপুরে আমার অফিসে আসতে বলিস।’
‘অফিসে কেন?’ নুযহাতের জিজ্ঞাসা।
‘ওর সাথে একটু সিরিয়াস বিষয়ে কথা বলতে চাই।’
‘ঠিক আছে, বাবা। ওকে অফিসেই যেতে বলব।’ চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ফেলল নুযহাত। ‘বাবা, চা খাবে?’
‘হ্যাঁ, দে।’
নুযহাত চা আনতে গেল। চোখে-মুখে খেলা করছে আনন্দ।
রফিক সাদির একটু বিষণ্ণ লাগছে। আসলে এত তাড়াতাড়ি তিনি মেয়ের বিয়ে নিয়ে ভাবছিলেন না। মেয়েটার বিয়ে হলে বড্ড একা হয়ে যাবেন। কিন্তু সবারই একটা নিজস্ব জীবন আছে। নুযহাতেরও অবশ্যই অধিকার আছে নিজের মত করে জীবনটাকে সাজিয়ে নেয়ার।
আবারও চোখে পানি এল তাঁর। দ্রুত চোখের পানি মুছলেন।
মেয়েকে চোখের পানি দেখাতে চান না রফিক সাদি।
দুই
ছেলেটির বসার ভঙ্গিটা বেশ অদ্ভুত। একদম সটানভাবে চেয়ারে বসে আছে। মনে হচ্ছে যেন সবে মাত্র আর্মির ট্রেনিং নিয়ে ফিরেছে। গায়ের রং শুধু কালো বললে ভুল হবে, পাতিলের তলাও তার চেয়ে উজ্জ্বল। চোখে কোনও প্রশ্ন বা উত্তেজনার ছাপ নেই। তাকিয়ে আছে একদৃষ্টিতে। পেশিবহুল হাতদুটো রেখেছে টেবিলের উপর। নিশ্চয়ই নিয়মিত ব্যায়াম করে। এমন শরীর বানানো চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। রফিক সাদির দৃষ্টি জয়ের শরীরে ঘুরে বেড়াতে লাগল।
হাসিমুখে বলল জয়, ‘আপনি আমাকে আজ দেখা করতে বলেছিলেন।’
‘তুমি জয়?’
‘হ্যাঁ।’ কোনও সামাজিক সম্ভাষণের মধ্যে যায়নি জয়। তার কথাবার্তা একদম সরাসরি।
রফিক সাদির কেমন যেন অন্যরকম লাগছে। ভেবেছিলেন জয় ছেলেটা নার্ভাস থাকবে, উল্টো তাঁর নিজেরই নার্ভাস লাগছে। পরিস্থিতি হালকা করার জন্য বললেন, ‘তোমার বাবা কী করেন?’
জয়ের চোখ কিছুটা সরু হয়ে এল। ‘বাবার নানা ধরনের ব্যবসা আছে।’
‘ও। তোমাদের বাসা কোথায়?’
‘ময়মনসিংহের কাছে, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে এলেমদারি নামে একটা ছোট বন আছে।’
‘এলেমদারি বনের নাম শুনেছি।’
‘এলেমদারি বনের মধ্য দিয়ে আধা পাকা রাস্তা চলে গেছে। সেই রাস্তা ধরে পশ্চিম দিকে ১৫-২০ মিনিট হাঁটলেই হাতের ডান পাশে আমাদের বাড়ি দেখতে পাবেন।’
‘বনের মধ্যে বাড়ি?’
‘বন এখন আর আগের মত ঘন নেই,’ আশ্বাসের ভঙ্গিতে বলল জয়। ‘আমার দাদা ইংরেজদের কাছ থেকে নিলামে এই বনের জায়গাটা কিনে নেন, তারপর সেখানে বাড়ি তৈরি করেন। গত সত্তর বছর ধরে আমরা ওখানে আছি।’
‘কিন্তু একদম একা-একা বনের মধ্যে থাকো, কোনও সমস্যা হয় না?’
‘একা কোথায়? আমাদের ওখানে আরও অনেকগুলো বাড়ি উঠেছে। বাবা বেশ খানিক জায়গা ইতিমধ্যে বিক্রিও করে দিয়েছেন। তবে সমস্যা একটা আছে।’
‘কী সমস্যা?’
‘বনবিভাগ এলেমদারি বনের বেশিরভাগ জায়গা নিজেদের বলে দাবি করছে। এজন্য আদালতে মামলা চলছে। তবে আশা করি আমরাই জিতব।’
জয়ের আত্মবিশ্বাসটা চোখ এড়াল না রফিক সাদির। ‘তো একদিন তোমার বাবা-মাকে আমাদের বাসায় আসতে বলো।’
‘আমার মা-বাবা তেমন একটা বাইরে বেরুতে চান না। তার চেয়ে আপনি একদিন আসুন আমাদের বাসায়। জায়গাটা আপনার ভাল লাগবে।’
জয়ের বলার মধ্যে কিছু একটা ছিল। রফিক সাদির মনে হলো, আসলেই সেখানে যাওয়া দরকার।
‘আমি তা হলে আজ উঠি।’
‘হ্যাঁ, ঠিক আছে। তোমার বাবার মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে যাও।’
‘আমাদের ওখানে মোবাইলের নেটওয়ার্কে সমস্যা আছে। তাই সবসময় মোবাইলে পাওয়া যায় না। এই নিন বাবার নাম্বার।’
জয় পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে দিল।
তবে কি আগেভাগেই মোবাইল নাম্বার লিখে এনেছে?
ভাল বুদ্ধি তো ছেলেটার!
জয় চলে যাওয়ার পর রফিক সাদি কাগজটার দিকে তাকালেন। জয় যে মোবাইল নাম্বারটা দিয়ে গেছে তাতে দুটো ডিজিট কম।
কয়েক মুহূর্ত পর রফিক সাদির মুখে ফুটে উঠল চিন্তার ছাপ।
তিন
‘বাবা, তুমি এলেমদারি কবে যাবে?’
‘কবে যাব এখনও ঠিক করিনি। আগে জয়ের বাবা-মা’র সাথে কথা বলি।’
‘ইয়ে…মানে, বাবা, বিয়ের কথা একটু দ্রুত এগুলে ভাল হত।’
রফিক সাদি কিছুটা বিরক্ত হয়ে মেয়ের দিকে তাকালেন। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিলেন। ‘ঠিক আছে, মা। দ্রুতই করব। জয়কে বল, তার মা-বাবাকে দিয়ে আমাদের বাসায় প্রস্তাব পাঠাতে। ছেলেপক্ষ বিয়ের প্রস্তাব না পাঠালে, কথাবার্তা এগোবে কীভাবে?’
কঠিন গলায় নুযহাত বলল, ‘বাবা, ওঁরা কেউ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসবেন না। তোমাকেই ওঁদের বাসায় যেতে হবে।’
‘আমি প্রস্তাব নিয়ে যাব!’
‘হ্যাঁ। সেকালের ধারণা নিয়ে বসে থাকলে তো মুশকিল, বাবা। ছেলেপক্ষকেই সবসময় প্রস্তাব পাঠাতে হবে, এমন কোনও লিখিত নিয়ম আছে?’
‘তুই এত রেগে-রেগে কথা বলছিস কেন?’
‘আমি মোটেই রেগে কথা বলছি না,’ চেঁচিয়ে বলল নুযহাত। ‘তোমার স্বার্থপরতায় অবাক হচ্ছি শুধু!’
‘স্বার্থপরতা?’ বিস্ময়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন রফিক সাদি।
‘হ্যাঁ। তুমি মনে করো, আমার বিয়ে হলে তুমি একা হয়ে যাবে। তাই এ ব্যাপারে তোমার কোনও আগ্রহ নেই।’
নুযহাতের কথায় খুব কষ্ট পেলেন রফিক সাদি। বললেন, ‘মা রে, তুই হয়তো ঠিকই বলেছিস, তোর বিয়ে হয়ে গেলে আমি একা হয়ে যাব। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি খুব দ্রুতই জয়ের সাথে তোর বিয়ে দেব।’
নুযহাত বাবার দিকে না তাকিয়ে দ্রুত রুম থেকে বের হয়ে গেল। রফিক সাদি লক্ষ করলেন, তার হাতে বেশ কয়েকটা তাবিজ সদৃশ জিনিস বাঁধা। তিনি সেগুলো তেমন গ্রাহ্য করলেন না। নিশ্চয়ই নতুন ফ্যাশন। কিন্তু মেয়েটা হঠাৎ এত খেপে গেল কেন? সে কি কোনও সমস্যায় পড়েছে? হঠাৎ করেই নিজের স্ত্রীর কথা মনে হলো রফিক সাদির।
.
রাত কত হয়েছে জানেন না রফিক সাদি। ইজিচেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কেন জানি হঠাৎই ঘুমটা ভেঙে গেছে। মনে হলো ঘরের ভিতর কোনও ঝামেলা হয়েছে। ঝামেলাটা কী তিনি ঠিক ধরতে পারছেন না। মনের ভিতর কেমন যেন এক ধরনের অস্বস্তি। তিনি ধীর পায়ে নুযহাতের ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন। রুমে বাতি জ্বলছে। নিচু গলায় নুযহাত কারও সাথে মোবাইলে কথা বলছে। লুকিয়ে মেয়ের কথা শোনা এক ধরনের অপরাধ, তবু তিনি কৌতূহল দমাতে পারলেন না।
নুযহাত বলছে, ‘আমি বাবাকে বলেছি। বাবা দুই-একদিনের মধ্যেই তোমাদের বাসায় প্রস্তাব নিয়ে যাবেন।
ওপাশ থেকে কিছু বলা হলো।
নুযহাত করুণ গলায় বলল, ‘বুঝতে চেষ্টা করো, আমাদের বিয়ে হওয়াটা জরুরি। না, না, আমার বাবা কখনোই অমন মানুষ নন।’
আবার ওপাশ থেকে কিছু বলা হলো।
নুযহাত উত্তেজিত গলায় বলল, ‘কী? বাবা তোমার সাথে খারাপ আচরণ করেছেন? এ কথা আগে বলোনি কেন? ঠিক আছে, আমি বাবাকে কিছু জিজ্ঞেস করব না…’
কথোপকথন চলতে লাগল।
রফিক সাদির মনে হলো তিনি ভুল শুনেছেন। তিনি তো জয়ের সাথে কোনও খারাপ ব্যবহার করেননি। তা হলে এসব কথার মানে কী? একটু পরে তিনি নুযহাতের কান্নার শব্দ শুনলেন। নিচু স্বরে কাঁদছে মেয়েটা। রফিক সাদির মনের ভিতর ওলট-পালট হতে থাকল। ইচ্ছা হচ্ছে দরজা নক করে মেয়ের সমস্যা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে। কিন্তু মেয়েটা হয়তো এসব ভালভাবে নেবে না। তাই তিনি নিজ রুমে ফিরে গেলেন। কিন্তু বাকি রাত তাঁর ঘুম হলো না।
চার
সকালে রফিক সাদি বাসার সামনে ছোট বাগানে পায়চারি করছেন। ড্রাইভার মহসিন এসে পিছন থেকে সালাম দিল। ‘বড় ভাই, আসসালামুলাইকুম।’
পঁচিশ বছর ধরে মহসিন এই বাসায় আছে। রফিক সাদি নীচতলার দু’রুম মহসিনের জন্য ছেড়ে দিয়েছেন। মহসিন তার স্ত্রী, দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে সেখানে থাকে। বাড়ির ড্রাইভার হলেও রফিক সাদির সাথে তার এক ধরনের বন্ধুত্ব আছে। রফিক সাদিকে সে বড় ভাই বলে ডাকে।
‘অলাইকুম আসসালাম,’ বললেন রফিক সাদি।
‘কিছু নিয়ে ভাবছেন?’
অন্য কেউ হলে রফিক সাদি এড়িয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করতেন। কিন্তু মহসিনকে তিনি ছোট ভাইয়ের মতই মনে করেন।
‘কিছু বিষয় নিয়ে চিন্তায় আছি। তোমাকে সময় করে বলব।’
‘বুঝতে পারছি মামণিকে নিয়ে চিন্তা করছেন।’
‘মেয়ে বড় হলে বাবার চিন্তা তো বাড়েই, আর মা-মরা হলে তো বাবার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে।’
‘ভাই, আজ কি অফিসে যাবেন?’
‘মনে হয় না। অফিসের কাজে মন দিতে পারি না। ম্যানেজারই এখন সব দেখাশোনা করছে। তবে আজ বাইরে বের হব।’
‘কোথায় যাবেন?’
‘কিছুক্ষণ পরে বলছি।’
মহসিন লক্ষ করল, নুযহাত আসছে। এজন্যই হয়তো রফিক সাদি চুপ করে গেলেন। তিনি চোখের ইশারায় মহসিনকে চলে যেতে বললেন।
এক রাতেই নুযহাতের চেহারায় কেমন যেন একটা পরিবর্তন হয়ে গেছে। কোটরের মধ্যে ঢুকে গেছে চোখগুলো, এলোমেলো হয়ে আছে মাথার চুল, কয়েকটা ব্রণও উঠেছে মুখে। মনে হচ্ছে রাতে একটুও ঘুম হয়নি।
রফিক সাদি মেয়েকে দেখে ভিতরে-ভিতরে চমকে উঠলেও স্বাভাবিক গলায় বললেন, ‘মা, ঘুম ভাঙল?’
নুযহাত বাবার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মনে হলো বাবার কথা শুনতে পাচ্ছে না।
রফিক সাদি নিজেই আবারও বললেন, ‘আজই জয়দের বাসায় যাব ভাবছি। কিন্তু জয়ের বাবার মোবাইল নাম্বারটা আমার কাছে নেই। তুই জয়ের নাম্বারটা আমাকে দিস।’
‘জয়ের নাম্বার আমার কাছে নেই।’
‘কী? নাম্বার নেই!’ নিজের বিস্ময়টুকু লুকাতে পারলেন না তিনি।
‘হ্যাঁ। জয় মোবাইল ব্যবহার করে না।’
‘কাল রাতে না তুই জয়ের সাথে মোবাইলে কথা বলছিলি?’ ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।
‘তুমি কী করে জানলে?’ ভুরু কুঁচকে পাল্টা প্রশ্ন করল নুযহাত।
‘পানি খেতে ডাইনিং রুমে গিয়েছিলাম, তখনই মনে হলো তুই কারও সাথে কথা বলছিস।’
‘আমার মোবাইল কাল রাতে ড্রইংরুমে চার্জে দেয়া ছিল, আমি কাল রাতে কারও সাথে মোবাইলে কথা বলিনি,’ ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল নুযহাত।
‘ও, আচ্ছা। তা হলে হয়তো ভুল শুনেছি।’
‘তুমি আজই জয়দের বাসায় যাও। ওর সাথে আমার কথা হয়েছে, ওর বাবা- মা আজই তোমাকে যেতে বলেছেন। ‘
নুযহাতের কথা কেমন যেন খাপছাড়া লাগছে রফিক সাদির। একটু আগেই বলল, জয়ের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ হয় না, আবার বলছে, জয়ের সাথে কথা হয়েছে।
‘ঠিক আছে, যাব, মা।’
‘ঠিকানা জানো?’
‘হ্যাঁ, জয় বলেছিল, আমি খুঁজে নেব। চিন্তা করিস না।’
‘বাবা, এমনভাবে কথাবার্তা ঠিক করবে, যেন এক সপ্তাহের মধ্যে বিয়ে হয়ে যায়। কোনও অনুষ্ঠানের দরকার নেই।’
‘তুই আমার একমাত্র মেয়ে, তোর বিয়েতে কোনও অনুষ্ঠান হবে না? আর এক সপ্তাহের মধ্যেই বিয়ে হতে হবে কেন?’
‘আমি এত কিছুর ব্যাখ্যা তোমাকে দিতে পারব না।’
‘আচ্ছা, আমি আজই যাব। এক সপ্তাহ না, তার আগেই তোর বিয়ে দেব।’ রাগটা সামলানোর চেষ্টা করেন রফিক সাদি।
‘এলেমদারি বনে ঢুকলেই বেশ কিছু বাড়ি-ঘর দেখতে পাবে,’ বাবার ভ্রূক্ষেপে পাত্তা না দিয়ে বলল নুযহাত। ‘জঙ্গলের কিছু জায়গা সাফ করে গোটা দশেক পরিবার সেখানে বসবাস করছে। তাদের যে-কারও কাছে জিজ্ঞেস করলেই ঝমঝম কুঠি দেখিয়ে দেবে।’
‘ঝমঝম কুঠি?’
‘ওটাই জয়দের বাড়ি।’ কথা শেষ করেই ঘুরে হাঁটতে শুরু করল নুযহাত। রফিক সাদি লক্ষ করলেন পা টলছে মেয়েটার। একবারও পিছন ফিরে তাকাল না।
সাধনা – ৫
পাঁচ
মহসিন গাড়িটা ব্রেক করল। পিছন দিকে তাকিয়ে বলল, ‘ভাই, এটাই এলেমদারি বন।’
রফিক সাদি গাড়ি থেকে নামলেন। একটা ছোট সাইনবোর্ড নজরে পড়ল। সেখানে লেখা: ‘এলেমদারি বন। অবাঞ্ছিত ব্যক্তির প্রবেশ নিষেধ। গাড়ি বা কোনও যানবাহন নিয়ে ভিতরে ঢুকবেন না।’
রফিক সাদি বললেন, ‘তুমি গাড়িতেই থাকো। আমি এক ঘণ্টার ভিতর আসছি। আর যদি আরও দেরি হয়, তোমাকে আমি ফোনে জানাব।’
‘ঠিক আছে, ভাই।’
একটা আধপাকা সড়ক বনের মধ্যে চলে গেছে। রফিক সাদি সেই পথেই হাঁটা শুরু করলেন। বনের পরিবেশটা আশ্চর্যরকম নীরব। পাখির ডাক নেই, পাতার খসখস শব্দ নেই, এমনকী বাতাসের চঞ্চলতাও নেই। বুকের মধ্যে কেমন যেন কাঁপুনি উঠল তাঁর, পায়ের শব্দ যেন নীরবতা ছাপিয়ে বহুদূর ছড়িয়ে পড়ছে। কিছুদূর হাঁটার পর কিছু বাড়ি দেখতে পেলেন। সবগুলোই টিনের বাড়ি। তবে বাড়ির ভিতর থেকেও কোনও শব্দ আসছে না। রফিক সাদি একজন মধ্যবয়স্ক মানুষকে দেখে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। লোকটার মাথায় একটাও চুল নেই। সবসময় মাটির দিকে তাকিয়ে আছে। পরনে লুঙ্গি ছাড়া কিছু নেই। গলা থেকে তলপেট পর্যন্ত উল্কি আঁকা। অদ্ভুত ধরনের উল্কি। একটা মানুষের অবয়ব বলে মনে হচ্ছে। রফিক সাদির কেন জানি মনে হচ্ছে, এই অবয়বটাকে তিনি চেনেন। যেন উল্কি আঁকা মানুষটা রফিক সাদির দিকে তাকিয়ে হাসছে।
রফিক সাদি উল্কি থেকে দৃষ্টিটা সরিয়ে মানুষটার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘ঝমঝম কুঠিটা কোন্ দিকে?’
প্রশ্নটা শুনে মানুষটা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কোনও জবাব দিল না। মনে হচ্ছে কথাটা বুঝতে পারছে না।
রফিক সাদি তাগাদা দিলেন, ‘ঝমঝম কুঠিটা কোন্ দিকে?’
লোকটা এবারও জবাব দিল না। তবে তার চোখের উজ্জ্বলতা একটু বাড়ল। ইশারায় ডানদিকে যেতে বলল।
রফিক সাদি ডানদিকে হাঁটতে শুরু করলেন। আরও চার-পাঁচটা টিনের বাড়ি চোখে পড়ল। কোনও বাড়িতেই তেমন লোকজন চোখে পড়ছে না। মিনিট পনেরো হাঁটার পর ঝমঝম কুঠিটা দৃষ্টিগোচর হলো। পুরনো ধাঁচের বিশাল এক দোতলা বাড়ি। কোথাও-কোথাও খসে পড়েছে চুন ও পলেস্তারা। বাড়ির সামনে জন্মেছে রাজ্যের আগাছা। শ্যাওলাতে সবুজ রং ধারণ করেছে বাড়ির কিছু অংশ। সদর দরজাটা ধাক্কা দিলেন রফিক সাদি। কিছুক্ষণ পর বুড়ো মত এক লোক এসে দরজা খুলে দিল। পোশাক-আশাকে মনে হচ্ছে বাড়ির চাকর।
রফিক সাদি বললেন, ‘আমি রফিক সাদি। জয়ের বাবার সাথে দেখা করতে এসেছি। উনি কি আছেন?’
বুড়ো লোকটি মাথা দোলাল। শোনা যায় না প্রায়, এমন গলায় বলল, ‘আসুন। আমার সাথে দোতলায় আসুন।’
রফিক সাদি অনুসরণ করলেন লোকটিকে। ভুলও হতে পারে, তবে কেন যেন মনে হচ্ছে দোতলায় একটা মেয়ে কাঁদছে।
দোতলায় বাইরের এক রুমে তাঁকে বসতে দেয়া হলো। বেশ কিছু সময় পেরিয়ে গেল। ভিতর ঘর থেকে কারও উত্তেজিত কথা শোনা যাচ্ছে, একইসাথে পাওয়া যাচ্ছে এক মেয়ের চাপা কান্নার আওয়াজও। খানিকক্ষণ পর বাড়ির পরিবেশ কেমন যেন শান্ত হয়ে গেল। ঠিক তখন একজন পুরুষ এবং মহিলা ঘরে ঢুকলেন। রফিক সাদি বুঝতে পারলেন এঁরাই জয়ের মা-বাবা।
রফিক সাদি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘কেমন আছেন? আমি নুযহাতের বাবা।’
জয়ের বাবা মাথা দোলালেন। মাথায় কোনও চুল নেই। গা উদোম। ঘামে পুরো শরীর ভেজা।
রফিক সাদি লক্ষ করলেন, মানুষটার শরীরে উল্কি আঁকা। প্রথমে বনে ঢুকে যে লোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সেই লোকটার মত একই উল্কি।
জয়ের বাবা বললেন, ‘আমি সোলেমান গাজি। জয়নাল আপনার কথা আমাদের বলেছে।’
‘জয়নাল কে?’
‘জয়ই জয়নাল। আপনাদের কাছে জয়, আমাদের কাছে জয়নাল। হা-হা।’ সোলেমান গাজির হাসিটা যেন কেমন, পুরো শরীরে কাঁটা দিয়ে ওঠে।
‘আচ্ছা, আচ্ছা। আসলে ছেলে-মেয়ে দু’জন দু’জনকে পছন্দ করেছে, এখন বাবা-মা হিসাবে আমাদের দায়িত্ব ওদের বিয়ের ব্যবস্থা করা।’
‘দেন, বিয়ে দেন,’ কান চুলকাতে চুলকাতে বললেন সোলেমান গাজি।
‘হ্যাঁ, বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক করার জন্যই আসলে আমি এসেছি।’
‘দিন-তারিখ ঠিক করতে হবে না, আপনি একদিন মেয়েকে নিয়ে আসুন। সেদিনই বিয়ে হয়ে যাবে।’
‘আমি মেয়ে এখানে এনে বিয়ে দেব?’ রফিক সাদির বিস্ময় যেন সব সীমা অতিক্রম করল।
এবার জয়ের মা বললেন, ‘হ্যাঁ। আমরা বাইরে তেমন বের হই না। বিয়ে সংক্রান্ত এত ঝামেলা আমাদের পছন্দ নয়। আপনি মেয়ে সাজিয়ে এখানে নিয়ে আসবেন, বিয়ে হবে। তারপর থেকে মেয়ে আমাদের।’ আমাদের কথাটার উপর তিনি অনাবশ্যক জোর দিলেন।
রফিক সাদি কী বলবেন বুঝতে পারছেন না। ক্রমেই খারাপ হচ্ছে মেজাজ। এঁরা কি নির্বোধ?
এমন সময় হেলতে-দুলতে কেউ ঘরে ঢুকল। রফিক সাদি তাকিয়ে দেখলেন-জয়। জয়ের দিকে তিনি বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। মাথায় কোনও চুল নেই। গলা থেকে পেট পর্যন্ত উল্কি আঁকা। তবে একটা মানুষের অবয়বের পাশাপাশি শরীরে কিছু দুর্বোধ্য অক্ষর। জয়ের জিভ বের করা, মুখ থেকে লালা পড়ছে। বোকার মত এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।
জয়ের বাবা বিরক্তমুখে ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘তুই এখানে কেন?’ জয় কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলল, ‘ব্যথা করে। খুব ব্যথা করে। ছোট বাচ্চা যেমন কান্নার আগে ঠোঁট বাঁকিয়ে ফেলে, জয়ও তেমন ভঙ্গি করল।
সোলেমান গাজি ধমক দিয়ে বললেন, ‘খবরদার, কাঁদবি না। বজ্জাত।’
জয় বাবার ধমক শুনে বাচ্চাদের মত কাঁদতে লাগল।
জয়ের মা-ও ধমকে উঠলেন, ‘যা এখান থেকে!’
চোখ মুছতে-মুছতে চলে গেল জয়।
এমন পরিস্থিতিতে তাঁদের বিব্রত হওয়া স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু তাঁদের মুখে কোনও অস্বস্তির ছাপ দেখা গেল না। জয়ের মা নিরস গলায় বললেন, ‘মাঝে- মাঝে ছেলেটা কেমন যেন ছোট হয়ে যায়। পাগল-ছাগলের মত আচরণ করে।’ বলতে-বলতে তিনি হাসলেন। যেন ছেলে পাগল-ছাগল হওয়াতে তিনি মহাখুশি।
এমন সময় জয়ের চিৎকার করে কান্নার শব্দ শোনা গেল।
সোলেমান গাজি ও তাঁর স্ত্রী প্রায় দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন।
রফিক সাদির মনে কেমন যেন অজানা ভয় কাজ করছে।
এসব কী হচ্ছে!
তিনি ধীর পায়ে উঠে দাঁড়ালেন।
সোলেমান গাজির উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।
হঠাৎ রফিক সাদির সামনে এসে দাঁড়াল এক মেয়ে। আশ্চর্যের বিষয় মেয়েটার মাথায়ও কোনও চুল নেই। মুখে-গলায় ছোপ ছোপ রক্ত। কাঁপা গলায় ফিসফিস করে বলল, ‘আমাকে বাঁচান!’
রফিক সাদি বললেন, ‘মানে? কে তুমি?’
ভাঙা গলায় কাতর সুরে বলল মেয়েটি, ‘আমাকে মেরে ফেলবে! সত্যি আমাকে মেরে ফেলবে! আমাকে বাঁচান!’
‘আমি তোমার কথা বুঝতে পারছি না।’
মেয়েটা হাতজোড় করে বলল, ‘আপনি আমাকে নিয়ে চলুন। আমি আপনাকে পরে সব বুঝিয়ে বলব। চলুন।’
রফিক সাদি হতবুদ্ধির মত তাকিয়ে রইলেন।
এই মেয়ে পাগল নাকি? কেমন উদ্ভট কালো জোব্বা আকৃতির পোশাক পরে আছে। মুখ দিয়ে আসছে বিশ্রী গন্ধ। মনে হচ্ছে মদ জাতীয় কিছু খেয়েছে। কাঁধে ভ্যানিটি ব্যাগ। ব্যাগের চেন খোলা। এমন সময় সোলেমান গাজি ও তাঁর স্ত্রী ঘরে ঢুকে মেয়েটাকে দেখে চমকে উঠলেন। ‘তুই? তুই ঘর থেকে বের হয়েছিস? যা! ঘরে যা!’
মেয়েটা চিৎকার করে বলল, ‘না! আমি বাড়ি যাব! আমাকে যেতে দাও!’
সোলেমান গাজির চিৎকার শুনে বুড়ো চাকর এবং আরও দু’জন ছেলে ঘরে ঢুকল। ছেলে দু’জন মেয়েটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগল।
মেয়েটা চিৎকার করছে আর বলছে, ‘আমাকে বাঁচান! আমাকে বাঁচান! এরা আমাকে মেরে ফেলবে!’
ছেলে দু’জন তার হাত ধরে টানতে লাগল। তাদের জোরের কাছে হার মানবে না যেন মেয়েটা! সোলেমান গাজি ও তাঁর স্ত্রীও মেয়েটাকে চেপে ধরলেন। মেয়েটার ব্যাগটা নীচে পড়ে যেতেই মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল বিভিন্ন জিনিস। টেনে হিঁচড়ে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হলো মেয়েটাকে। এখনও শোনা যাচ্ছে তার চিৎকার। বোঝা যাচ্ছে কেউ তাকে মারছে।
রফিক সাদি লক্ষ করলেন, মেঝেতে মেয়েটার চিরুনি, ছোট আয়না, ক্লিপ, কিছু কাগজপত্র ছড়িয়ে আছে। তিনি নিচু হয়ে লেমিনেটিং করা একটা কাগজ তুলে নিলেন। মনে হচ্ছে ওটা আইডি কার্ড। এক ঝলক চেয়েই তিনি দ্রুত পকেটে পুরলেন আইডি কার্ডটা। হঠাৎ কমে এল মেয়েটার চিৎকার।
সোলেমান গাজি ও তাঁর স্ত্রী আবার ঘরে ঢুকলেন।
সোলেমান গাজি বললেন, ‘ও আমার দূরসম্পর্কের বোনের মেয়ে। আমার কাছেই মানুষ হয়েছে। মাথার ঠিক নেই।’
রফিক সাদি দুর্বলভাবে মাথা নাড়লেন। এখান থেকে বেরুতে পারলে বাঁচেন। ‘আমি আজ উঠি।’
‘আচ্ছা। ঠিক আছে।’
রফিক সাদিকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে এলেন না কেউ। বাড়ি থেকে বের হয়ে তাঁর মনে হলো, কিছু একটা যেন অনুসরণ করছে। আনমনেই হাঁটতে-হাঁটতে বাড়ির পিছন দিকে চলে এলেন। কী আশ্চর্য, পিছনে অনেকখানি খোলা জায়গা। দূরে কবরস্থান আছে বলে মনে হচ্ছে। কবরস্থানের পাশেই মাঠ। বোঝা যাচ্ছে, নিয়মিত জায়গাটার পরিচর্যা করা হয়। বেশিক্ষণ সেখানে থাকার সাহস হলো না রফিক সাদির। তিনি হনহন করে হাঁটতে শুরু করলেন। এবার প্রতিটা বাড়ির মানুষগুলোকে ঘরের বাইরে দেখতে পেলেন। সবাই একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। সবারই গা উদোম এবং সবার শরীরেই সেই অদ্ভুত উল্কি। রফিক সাদির কেন জানি মনে হচ্ছে, মানুষগুলো হিংস্র জন্তুর মত ঝাঁপিয়ে পড়বে। সবার চোখের দৃষ্টি কঠোর থেকে কঠোরতম হচ্ছে।
রফিক সাদি মাথা নিচু করে হাঁটতে লাগলেন।
তাঁর পিছু নিল কয়েকজন।
পিছনে না তাকিয়ে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলেন তিনি। দূর থেকে দেখলে মনে হবে, তিনি রীতিমত দৌড়াচ্ছেন। একসময় বন পেরিয়ে চলে এলেন মূল রাস্তায়। পিছনে চেয়ে কাউকে আর দেখতে পেলেন না।
ছয়
রফিক সাদিকে হাঁপাতে দেখে পানি নিয়ে ছুটে এল মহসিন।
এক নিঃশ্বাসে পানিটুকু শেষ করলেন সাদি।
মহসিন চিন্তিত গলায় বলল, ‘ভাই, কোনও সমস্যা? প্রায় আধঘণ্টা ধরে আপনার মোবাইলে চেষ্টা করছি, কিন্তু ঠিকমত নেটওয়ার্ক পাওয়া যাচ্ছে না।’
‘কোনও সমস্যা নেই,’ নিজেকে শান্ত করে বললেন রফিক সাদি। একটু বিরতি দিয়ে জানতে চাইলেন, ‘তা, তুমি আমাকে ফোন করছিলে কেন?’
‘ইয়ে…মানে…ভাই, আপনি এলেমদারি বনে যাওয়ার পর আমি হাইওয়ে ধরে খানিকটা সামনে গিয়েছিলাম। মাইল খানেক দূরে কয়েকটা চায়ের দোকান পেলাম। ওখানে বসে চা খাচ্ছিলাম। চায়ের দোকানদারের সাথে কথা প্রসঙ্গে হঠাৎ এলেমদারি বনের কথা উঠল। আমার কথায় যেন চমকে গেল লোকটা। বলল যে, এই বন নিয়ে প্রচলিত আছে অনেক কথা। কী প্রচলিত আছে তা কেউ বলতে চাইল না। তবে আকার-ইঙ্গিতে মনে হলো, অনেক মানুষ নিখোঁজ হয়েছে এই বনে। ঝমঝম কুঠিতে নাকি ভূত থাকে, এটাও মুখ ফসকে বলে ফেলল একজন। আমি এসব শুনে আর দেরি করিনি, গাড়ি নিয়ে দ্রুত এলেমদারি বনের সামনে এসে আপনাকে ফোন করেছি। আপনাকে যখন ফোনে পাচ্ছিলাম না, তখন কাঁপতে লাগল বুক।’
‘মহসিন, বুক তো আমারও কাঁপছে। তবে নিজের জন্য যত না, তার চেয়ে বেশি আমার মেয়ের জন্য।’
‘ভাই, আমাকে বলবেন কী হয়েছে?’
খানিক ভেবে রফিক সাদি বললেন, ‘হ্যাঁ, বলব।’
রফিক সাদি সব খুলে বললেন মহসিনকে।
নুযহাতের অদ্ভুত আচরণ, এলেমদারি বন এবং ঝমঝম কুঠির আজব সব ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিলেন।
মহসিন বলল, ‘ভাই, এদের তো স্বাভাবিক মানুষ বলে মনে হচ্ছে না।’
‘হ্যাঁ, আমারও তা-ই ধারণা, কিন্তু কী করব বুঝতে পারছি না। নুযহাত আমার কথা বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না।’
‘আমি একজন মানুষকে চিনি, পত্রিকায় তাঁকে নিয়ে কিছু লেখাও পড়েছি। কেন জানি মনে হচ্ছে, তিনি এই সমস্যার ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবেন। তাঁর কাছে একবার যাবেন নাকি?’
‘কী ধরনের সাহায্য?’
‘উনি ভৌতিক এবং রহস্যের বিষয়গুলোতে বিশেষজ্ঞ। মানুষকে এসব ব্যাপারে সাহায্য করেন।’
‘তাঁর নাম?’
‘আনোয়ার।’
‘তুমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে চেনো?’
‘আমাদের গ্রামে একবার গিয়েছিলেন। সেখানেই পরিচয় হয়েছিল তাঁর সাথে। আমাদের গ্রামে শিগব নামে এক অপদেবতার উপদ্রব হয়েছিল, উনি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সবাইকে রক্ষা করেছিলেন।’
‘চলো, তা হলে তাঁর কাছে যাই। এতদিন এই বিষয়গুলো বিশ্বাস করিনি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বিশ্বাস করতেই হবে।’
সাত
আনোয়ারদের ছাদের চিলেকোঠায় বসে আছেন রফিক সাদি ও মহসিন। আনোয়ারের মুখে বিরক্তির ছাপ স্পষ্ট। কয়েকটা পত্রিকায় তাকে নিয়ে ফিচার হয়েছে। এরপর থেকেই বাসায় মানুষজনের আনাগোনা বেড়ে গেছে। অনেকেই বিচিত্র সমস্যা নিয়ে তার কাছে আসছে। কিন্তু সে তো বেশিরভাগ সমস্যারই সমাধান দিতে ব্যর্থ। আর তার মূল কাজ রহস্য বা ভয়ের পিছনে ছোটা, মানুষকে সাহায্য করা নয়।
মহসিনকে চিনতে পেরেছে আনোয়ার। পাতাকাটা গ্রামে লোকটির সাথে দেখা হয়েছিল।
রফিক সাদির সাথে আনোয়ারের পরিচয় করিয়ে দেয়ার পর রফিক সাদি পুরো ঘটনাটা আনোয়ারকে বললেন।
মন দিয়ে শুনল আনোয়ার। কথার শেষে বেশ কয়েকটা প্রশ্নও করল।
‘আচ্ছা, আপনি তো বললেন নুযহাতের হাতে তাবিজের মত কিছু জিনিস দেখতে পেয়েছেন। জয়ের হাতে বা শরীরের কোথাও কি এমন কিছু দেখেছিলেন?’
চমকে উঠলেন রফিক সাদি। আরে, তাই তো! জয়ের হাতেও কয়েকটা তাবিজ বাঁধা ছিল। জবাব দিলেন, ‘হ্যাঁ। তার হাতেও ছিল।’
‘আপনি বলছিলেন এলেমদারি বনে যারা বাস করে, সবার শরীরে এক ধরনের উল্কি আঁকা এবং উল্কিটা মানুষের অবয়বের। ভেবে দেখুন তো, আপনার পরিচিত কোনও মানুষের সাথে অবয়বটার মিল আছে?’
‘আমার বারবার মনে হচ্ছিল অবয়বটা আমি চিনি। কিন্তু ….’
‘আচ্ছা, ঠিক আছে, পরে কিছু মনে পড়লে আমাকে তা জানাবেন। আমার মোবাইল নাম্বার রেখে দিন। আর আপনার মেয়ের বিয়ের চিন্তা আপাতত বাদ রাখুন।’
‘মেয়েটা তো বিয়ে নিয়ে কেমন পাগলের মত করছে।’
‘তাকে বোঝান, একটু ধৈর্য ধরতে বলুন। আর শুরুতেই এলেমদারির লোক খারাপ বা ভাল, এসব ভাববেন না। মানুষের কথায় কান দেবেন না। আমি নিজে জায়গাটায় যাব। আশা করছি, দেরি না করেই গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য আপনাকে জানাতে পারব।’
‘ঠিক আছে। তবে আপনার ওখানে যাওয়াটা একটু বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যাবে না?’
‘চিন্তা করবেন না। আমি নির্বোধ নই, নিজের সুরক্ষার ব্যবস্থা করেই যাব। আপনিও আমার সাথে যাবেন।’ একটু থেমে আনোয়ার বলল, ‘ও, আরেকটা কথা, আপনি বলছিলেন ওখানে একটা মেয়েকে দেখেছেন। তার নাম জানতে পেরেছেন বা অন্য কিছু?’
‘না, আমি ওই সময়ে হকচকিয়ে গিয়েছিলাম, তাই এসব জিজ্ঞেস করার কথা মাথায় আসেনি। তবে…’
‘তবে কী?’
‘সম্ভবত মেয়েটার একটা আইডি কার্ড আমি আনতে পেরেছি।’
‘গুড, কোথায় সেই আইডি কার্ড?’
রফিক সাদি আইডি কার্ডটা বের করে আনোয়ারের হাতে দিলেন।
ভাল করে কার্ডটা দেখল আনোয়ার। ইডেন কলেজের রসায়ন বিভাগের এক মেয়ের আইডি কার্ড। নাম ফারহানা সুলতানা।
‘আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, বিষয়টা নিয়ে আজ থেকেই কাজে নামব আমি।’ আনোয়ারের কথায় রফিক সাদি তেমন আশ্বস্ত হননি, বেশ বোঝা যাচ্ছে। আরও দু’চার কথার পর উঠে পড়লেন তিনি।
রফিক সাদি ও তাঁর ড্রাইভার বিদায় হওয়ার পর বন্ধু শাহেদ চৌধুরীকে ফোন করল আনোয়ার।
শাহেদ চৌধুরী ডিবি পুলিশ অফিসার। বেশ কিছু রোমহর্ষক কেস সমাধান করে নিজেকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে। স্কুল ও কলেজে একসাথে পড়েছে আনোয়ার ও শাহেদ। অনার্স থেকে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আলাদা হলেও মনের দূরত্ব বাড়েনি।
‘শাহেদ, আনোয়ার বলছি। ব্যস্ত নাকি?’
‘কেমন আছিস, আনোয়ার? না, তেমন ব্যস্ত না।’
‘ভাল আছি। তোর সাহায্য দরকার।’
‘কী বিষয়ে সাহায্য?’
‘এখন তোকে সব বলতে পারছি না। আপাতত এক মেয়ে সম্পর্কে খোঁজ দরকার।’
‘কোন্ মেয়ে?’
‘ইডেন কলেজে পড়ে, রসায়ন বিভাগে, নাম ফারহানা সুলতানা।’
‘আচ্ছা? প্রেমঘটিত কোনও ব্যাপার নাকি?’
‘হা-হা, আরে না। সিরিয়াস ব্যাপার।’
‘তা হলে বল, এই মেয়ে সম্পর্কে কী জানতে চাস?’
‘আমি জানতে চাই মেয়েটা কি এখন কলেজে যাচ্ছে, নাকি সে নিখোঁজ। আর সে যদি নিখোঁজ হয়ে থাকে, তো এ ব্যাপারে থানায় কোনও জিডি বা মামলা করা হয়েছে কি না।’
‘আচ্ছা, সমস্যা নেই, আমি খোঁজ লাগাচ্ছি। কিছু জানতে পারলে তোকে জানাব।’
‘হ্যাঁ। একটু দ্রুত জানাতে চেষ্টা করিস।’
‘তুই পুরো ব্যাপারটা বললে হয়তো তোকে আরও নানা দিক দিয়ে সাহায্য করতে পারতাম।’
‘আগে নিজে পুরো ব্যাপারটা বুঝে নিই, তারপর অবশ্যই তোকে বলব।’
‘আচ্ছা।’
‘রাখছি এখন। বাই।’
.
রাত হয়ে গেছে।
ল্যাপটপের সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে আনোয়ার।
বেশ কিছু বিষয়ে ইন্টারনেট থেকে জানা দরকার।
আন্দাজ করতে পারছে অনেক কিছুই, তবে পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।
কালকেই সে এলেমদারি বনে যাবে।
তবে একা নয়, রফিক সাদি এবং ড্রাইভার মহসিনকে নিয়ে যাবে। বন্ধু শাহেদকে বলে যাবে, তারা ফিরে না এলে যেন এলেমদারি বন তথা ঝমঝম কুঠিতে অভিযান চালায়।
ফোন করে রফিক সাদিকে প্রস্তুত থাকতে বলল আনোয়ার।
সকালে দেরি না করে রওয়ানা হবে ওরা ওই বনের উদ্দেশে।
আট
এলেমদারি বনের মূল সড়কের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আনোয়ার এবং রফিক সাদি।
মহসিন বলল, ‘ভাই, আমি কি আপনাদের সাথে আসব?’
‘না,’ বলল আনোয়ার, ‘আপনি গাড়ি নিয়ে সামনে এমন কোথাও চলে যান, যেখানে লোকবসতি আছে। আমরা কাজ শেষে আপনাকে ফোন দেব।’
‘কিন্তু নেটওয়ার্কের তো বড্ড সমস্যা।’
একটা কার্ড বের করে মহসিনের হাতে দিল আনোয়ার। ‘বনের মধ্যে নেটওয়ার্কের সমস্যা হতে পারে, তবে বনের বাইরে পাকা সড়কে তো সমস্যা হবে না। আমরা সড়কে এসেই আপনাকে ফোন দেব। আর যদি দেখেন বিকালের মধ্যে ফোন দিইনি, তবে আপনি এই নাম্বারে ফোন দেবেন। এটা ডিবি পুলিশ অফিসার শাহেদ চৌধুরীর নাম্বার।’
মহসিন নিতান্ত অনিচ্ছায় রাজি হলো। তারও যাওয়ার ইচ্ছা ছিল।
রফিক সাদি সঙ্গে করে নিজের লাইসেন্স করা রিভলভার নিয়ে এসেছেন। কোনও কাজে লাগবে কি না জানেন না, তবু মনের জোর বাড়াতে নিয়ে এসেছেন ওটা।
.
এলেমদারি বনে ঢুকে রফিক সাদির গলায় এবং ঘাড়ে কালো রং দিয়ে কয়েকটা বৃত্ত এঁকে দিল আনোয়ার।
রফিক সাদি আপত্তি করলেন না।
‘আপনি আজকে দৃঢ় পায়ে হেঁটে যাবেন,’ বলল আনোয়ার, ‘কারও দিকে তাকাবেন না। চিন্তা, ভয় এসব কিছুকেই মাথায় স্থান দেবেন না।’
মাথা নাড়লেন রফিক সাদি। আনোয়ারকে দেখে ভয়টাও এখন অনেকটা কমে গেছে। তবে কিছুটা অস্বস্তি নিয়ে বললেন, ‘কিন্তু জয়ের বাবা-মা যদি জিজ্ঞেস করেন, আজ আবার কেন এলাম? বা আপনাকেই বা কেন নিয়ে এলাম?’
‘বলবেন, আপনি মেয়েকে এখানে নিয়ে আসতে রাজি হয়েছেন। বিয়েতে আপনার কয়েকজন আত্মীয় উপস্থিত থাকবে। এসব কথা ফাইনাল করতেই আজ এসেছেন। আর আমার কথা জিজ্ঞেস করলে বলবেন, আমি আপনার ভাগ্নে। বিয়ের কথাবার্তা যখন চলছে, একজন আত্মীয় তো সাথে আসতেই পারে।’
‘ঠিক আছে। চলুন, এগোনো যাক।’
‘আমাকে তুমি করে বলবেন,’ হাসতে-হাসতে বলল আনোয়ার, ‘আমি কিন্তু আপনার ভাগ্নে। ভাগ্নেকে আপনি করে বললে কিন্তু ধরা পড়ে যাবেন।’
হাসিতে যোগ দিলেন রফিক সাদিও।
গুমোট পরিবেশটা যেন একটু হালকা হলো।
দু’জন হেঁটে চলেছে বনের ভিতর দিয়ে, এমন সময় এক লোককে দেখতে পেল আনোয়ার। তার শরীরের উল্কি ভাল করে লক্ষ্য করল। এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। লোকটা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাদের দিকে। হাতে মাছ ধরার কোঁচ।
আনোয়ার হাঁটছে, কাঁধে ঝুলছে ব্যাগ।
কিছুক্ষণ পর ঝমঝম কুঠিতে পৌঁছে গেল ওরা। পথিমধ্যে আর কোনও মানুষের দেখা পায়নি। বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে বলল আনোয়ার, ‘কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না। চলুন, এই সুযোগে বাড়ির পিছন দিকটা চক্কর দিয়ে আসি।’
রফিক সাদি সায় দিলেন।
বাড়িটা ঘুরে পিছন দিকে এসে চারপাশ ভাল করে লক্ষ্য করল আনোয়ার। জায়গাটা বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কিন্তু এক জায়গায় এলোমেলোভাবে পড়ে আছে কিছু জিনিস। তার ভিতর রয়েছে বেশ কিছু কাগজ, ব্যাগ, পলিথিন ইত্যাদি।
কয়েকটা খালি রক্তের ব্যাগ দেখল আনোয়ার। দেরি না করে দুটো রক্তের ব্যাগ পুরে ফেলল নিজের ব্যাগে।
অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন রফিক সাদি, ‘এসব ময়লা জিনিস ব্যাগে ভরছ কেন?’
কিছু না বলে হাসল আনোয়ার।
বাইরে থেকে দেখা যায় না কবরস্থানটা। ভিতরে ঢুকে ঘুরে দেখল ওরা। থমথমে পরিবেশ, কেমন যেন ভয়ের অনুভূতি হবে যে-কারও।
আনোয়ার সাইনবোর্ডে দেখল: ‘পারিবারিক কবরস্থান।
কবরস্থান ছাড়িয়ে একটু দূরে যাওয়ার পর আনোয়ার দেখতে পেল এক মাঠ। এক মাথায় ছোটখাট মঞ্চের মত জায়গা। ঠিক এমন সময় রাশভারী গলায় কেউ বলল, ‘আপনারা এখানে কী করছেন?’
রফিক সাদি দেখলেন, তাঁদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে সেই বুড়ো চাকরটা। হাসিমুখে বললেন রফিক সাদি, ‘আসলে সোলেমান গাজি সাহেবের কাছে এসেছি। ভাবলাম, বাড়িতে ঢোকার আগে জায়গাটা একটু ঘুরে দেখি।’
‘কাজটা ঠিক করেননি। এটা কবরস্থান এলাকা। পবিত্র জায়গা। অনুমতি না নিয়ে এখানে ঘোরাঘুরি করে অন্যায় করেছেন। চলেন, বাড়ির ভিতরে চলেন।’
.
আনোয়ার আর রফিক সাদি দোতলার ঘরে বসে আছে। সামনে বসে আছেন সোলেমান গাজি ও তাঁর স্ত্রী। আগের দিনের মত ঘোরাঘুরি করছে জয়ও। আজও মাথাটা একদিকে কাত হয়ে আছে, মুখ দিয়ে ঝরছে লালা। আজকে সোলেমান গাজির চোখ দিয়ে যেন বের হচ্ছে রক্ত। চেঁচিয়ে বললেন, ‘আপনি আবার কী মনে করে? আর বাড়ির পিছনে ঘুরঘুর করছিলেন কেন?’
‘আসলে বিয়ের বিষয়টা ফাইনাল করতে এসেছিলাম। আমার ভাগ্নে বাড়ির আশপাশে একটু ঘুরে দেখতে চাইছিল, তাই…’
‘আবার ফাইনালের কী আছে? বললাম না একদিন মেয়েকে নিয়ে আসবেন, বিয়ে দিয়ে দেব।’ কঠোর গলায় সোলেমান গাজি বললেন, ‘না, আপনাদের সাথে পোষাবে না। আপনার মেয়ের সাথে আমার ছেলের বিয়ে দেব না।’
মুখে একটা কষ্টের ছাপ ফুটিয়ে তুললেও মনে-মনে খুশি হলেন রফিক সাদি। বললেন, ‘আমরা কিছু অন্যায় করেছি?’
‘আপনাদেরকে আমার পছন্দ হয়নি, একটুও না। আর আপনি গলায় এসব কী লাগিয়েছেন, খুব বিশ্রী।’ সোলেমান গাজি নীচের দিকে তাকিয়ে কথা বলছেন। মনে হচ্ছে রফিক সাদির সাথে কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করছেন।
মন দিয়ে জয়কে লক্ষ্য করছে আনোয়ার, মনে অনেক প্রশ্ন। জয়কে দেখে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছে। ইশ্, আরেকটু সময় যদি কবরস্থানটা ঘুরে দেখা যেত।
আনোয়ারকে পেয়ে কি না কে জানে, রফিক সাদি আজকে অনেক বেশি নিশ্চিন্ত বোধ করছেন। মনে কোনও ভয় দানা বাঁধছে না। তিনি স্পষ্ট গলায় বললেন, ‘আপনার ভাগ্নি কেমন আছে? কোথায় সে?’
ঘরের ভিতর যেন সবকিছু থমকে গেল।
সোলেমান গাজি চোখ সরু করে বললেন, ‘তাকে কী দরকার? সে নিজের ঘরে ঘুমাচ্ছে। আপনারা আজ আসুন।’ এই কথাগুলোও মেঝের দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি।
মুখ কালো করে উঠে পড়লেন রফিক সাদি। মনে-মনে বেশ প্রফুল্ল অনুভব করছেন।
হঠাৎ করে বলল আনোয়ার, ‘একটু বাথরুমে যাব। বাথরুমটা কোন্ দিকে?’
সোলেমান গাজির মুখ থমথমে হয়ে গেল। নিতান্ত অনিচ্ছায় বাথরুমটা দেখিয়ে দিলেন।
বাথরুমে যাওয়া আনোয়ারের উদ্দেশ্য নয়, একটু ঘুরে দেখবে চারপাশ। ধীর পায়ে বাথরুমের দিকে চলেছে আনোয়ার, দেখতে পেল পাশাপাশি পাঁচ-ছয়টা রুম। প্রতিটা রুমের দরজা বন্ধ করা। এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে কিছু চুল। মেঝেতে লেপ্টে রয়েছে কালো কালি। ঘরে ধূপের গন্ধ। তীব্র আলোতেও অন্ধকার বলে মনে হচ্ছে ঘরগুলোকে।
বাথরুমে ঢুকে আনোয়ারের প্রচণ্ড বমি এল। মেঝেতে নিথর পড়ে আছে এক মেয়ে, কেশহীন মাথাটা বিচ্ছিন্ন, রক্তে ভেসে যাচ্ছে পুরো শরীর। মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল ও, আর তখনই অদৃশ্য হয়ে গেল মেয়েটা।
তা হলে কি সব চোখের ভুল?
কোথায় যেন মেয়েটাকে দেখেছে বলে মনে হচ্ছে ওর। মনে হতে লাগল, পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা। যে-কোনও মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়বে আনোয়ারের উপর। চোখ বন্ধ করে ভাবতে চাইল সে, সব মিথ্যা, তাকে ভয় দেখাতে চাইছে কেউ।
নয়
ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা দিয়েছেন রফিক সাদি আর আনোয়ার। আগের মত সপ্রতিভ নয় আনোয়ার, কিছু নিয়ে গভীর চিন্তায় আছে সে। রফিক সাদি বললেন, ‘আমার মেয়েটাকে ওঁরা বউ হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি নন। যাক, ভালই হলো। বেঁচে গেল আমার মেয়েটা।’
জবাব দিল না আনোয়ার।
‘কেন জানি মনে হচ্ছে অবসান হয়েছে আমার সব দুশ্চিন্তার, ভুলেও আর কোনও দিন ঝমঝম কুঠিতে পা দেব না।’
‘আমাকে ফার্মগেট নামিয়ে দেবেন,’ হুট করেই বলল আনোয়ার। তার কেন জানি মনে হচ্ছে রফিক সাদির মুখের হাসি থাকবে না।
রফিক সাদি বাড়িতে ঢুকতে না ঢুকতেই মহসিনের স্ত্রী করিমন এগিয়ে এল। চিন্তিতমুখে বলল, ‘মামণি একটা সুটকেস নিয়ে কোথায় যেন গেছেন। যাওয়ার আগে আপনাকে এই চিঠিটা দিয়ে গেছেন।’
রফিক সাদির মনে হলো সোজাভাবে দাঁড়াতে পারছেন না তিনি।
কাঁপা হাতে খুললেন চিঠিখানা।
বাবা,
আমি ঝমঝম কুঠিতে জয়ের কাছে চলে যাচ্ছি। সত্যি বলতে, কাজি অফিসে গিয়ে বেশ আগেই আমরা বিয়েটা সেরে ফেলেছি। তোমার সম্মানের কথা চিন্তা করে ভেবেছিলাম, দুই পরিবারের সম্মতিতে বিয়েটা আবার হোক। কিন্তু আমি জানতে পেরেছি, জয় আর জয়ের মা-বাবার সাথে তুমি দুর্ব্যবহার করেছ। তাঁরা কেউ তোমাকে পছন্দ করেননি। তাই জয় আমাকে ওর বাসায় চলে যেতে বলেছে। জয় ডাকলে আমি তো না গিয়ে পারি না, বাবা। আর তুমি অন্ধ, তাই হয়তো দেখতে পাওনি যে, আমি মা হতে চলেছি। আমার শরীর ভারী হয়ে যাচ্ছে। এজন্য বাইরে বের হওয়াও বন্ধ করে দিয়েছিলাম। মহসিন চাচা ও করিমন চাচী কিন্তু বিষয়টা টের পেয়েছিল। হয়তো ভয়ে তোমাকে বলতে পারেনি। আমি আমার স্বামী, সন্তান নিয়ে সুখেই থাকব, বাবা। তুমি আর আমাদের উৎপাত করতে এসো না।’
চিঠিটা শেষ করে মাথা ঘুরে পড়ে গেলেন রফিক সাদি। চিৎকার করে বললেন, ‘মা রে, তুই এটা কী করলি?’
.
শাহেদ চৌধুরী ফোন করেছে আনোয়ারকে।
‘ফারহানা সুলতানার খোঁজ পেয়েছি।’
‘হ্যাঁ, বল।’ তড়িঘড়ি করে বিছানায় উঠে বসল আনোয়ার।
‘ফারহানা নামের এই মেয়েটা দু’মাস আগে নিখোঁজ হয়। মেয়েটার মা-বাবা কেউ নেই। চাচার কাছে বড় হয়েছে। মেয়েটার চাচা ওর নিখোঁজ বিষয়ে নিউ মার্কেট থানায় জিডি করেছিলেন। তারপর আর তাঁদের তেমন মাথা-ব্যথা দেখা যায়নি। মা-বাবা না থাকলে যা হয় আর কী। মেয়েটার মোবাইল বন্ধ পাওয়া গেছে। পুলিশ তদন্ত করে দেখেছে, ফারহানার নীরব নামে এক ছেলের সাথে ফোনে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সম্ভবত নীরবের সাথে ফারহানার তেমন একটা দেখা হয়নি।’
একটু বিরতি দিয়ে শাহেদ বলল, ‘নিখোঁজ হওয়ার আগেও সে নীরব নামের ওই ছেলেটার সাথে কথা বলেছে। মোবাইল অপারেটরের মাধ্যমে পুলিশ নীরবের নাম-ঠিকানা বের করেছিল। কিন্তু সে ঠিকানায় গিয়ে পুলিশ বুঝতে পারে, নীরবের নাম-ঠিকানা, ন্যাশনাল আইডি সবই ভুয়া। এরপর পুলিশের কার্যক্রম অনেকটা স্তিমিত হয়ে গেছে।’
‘বাহ্! তুই তো অনেক তথ্য জোগাড় করেছিস!’
‘এখন বল, তুই ফারহানাকে চিনিস কীভাবে? ওর সম্পর্কে কিছু জানিস নাকি?’
‘সব তোকে বলব। তার আগে আরেকটা খবর বের করতে হবে। তোকে কাল সকালে ফোন দেব। আশা করি, কালকেই সব জানতে পারবি।’
শাহেদের সাথে কথা শেষ করে ইন্টারনেট ঘাঁটাঘাঁটি শুরু করল আনোয়ার। সামনেই রেখেছে রক্তের ব্যাগদুটো।
ব্যাগের ওপরের কাগজে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, একজনের নাম, ব্লাড নেয়ার তারিখ আর সময় লেখা।
ইন্টারনেটে বিভিন্ন ব্লাড ব্যাঙ্কের রেজিস্ট্রেশন নাম্বারের সাথে তা মিলিয়ে দেখে নিতে চাইল আনোয়ার।
বড় কোনও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাঙ্কের সাথে মিলছে না।
এবার কিছু বেসরকারি ক্লিনিকের ব্লাড ব্যাঙ্কের সাথে মিলিয়ে দেখতে লাগল।
কাঙ্ক্ষিত ফল পেতে সময় লেগে গেল, কিন্তু সফল হলো অবশেষে। বনানীর সোনালি ক্লিনিকের ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে নেয়া হয়েছে ওর পাওয়া ব্যাগ।
শাহেদকে নিয়ে কাল সকালেই যেতে হবে ওখানে, ঠিক করল আনোয়ার।
সাধনা – ১০
দশ
সোনালি ক্লিনিকের ব্লাড ব্যাঙ্কের দায়িত্বে যে লোকটা রয়েছে, সে বসে আছে টেবিলের ওপর পা তুলে। আনোয়ার ও শাহেদকে ঢুকতে দেখেও নির্বিকারভাবে পা তুলে রাখল টেবিলের ওপর। ইতিমধ্যে শাহেদকে সব খুলে বলেছে আনোয়ার।
শাহেদের মাথা পরিষ্কার, অল্পতেই সব বুঝে গেছে।
ব্লাড ব্যাঙ্কের লোকটার দিকে তাকিয়ে বলল আনোয়ার, ‘আমরা একটু দরকারে এসেছি। আপনার কাছ থেকে কিছু তথ্য দরকার।’
কুৎসিতভাবে গলা চুলকাতে চুলকাতে বলল লোকটা, ‘কী দরকার? ব্লাড-ফ্লাড এখন হবে না। বিশ্রামে আছি।’
‘তেরোই মার্চ, সন্ধ্যা সাতটায় জাহাঙ্গীর নামে একজন আপনাদের এখান থেকে ব্লাড নিয়েছিল। তার সম্পর্কে তথ্য দরকার।’
‘আমরা এসব তথ্য সংরক্ষণ করি না। আগে বাড়েন। যত্তসব!’
নিজের রিভলভারটা টেবিলে রাখল শাহেদ চৌধুরী। লোকটা কিছু বুঝে ওঠার আগে ঠাস করে চড় মেরে বসল।
যে রোগের যে ওষুধ।
আরেকবার হাত উঁচু করল শাহেদ, ‘হারামজাদা, পা নামিয়ে কথা বল!’
বিদ্যুতের গতিতে উঠে দাঁড়াল লোকটা। কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, ‘স্যর, মাফ করে দেন। আপনাদের চিনতে পারিনি।’
‘আমাদের নষ্ট করার মত সময় নেই,’ আনোয়ার বলল, ‘আমাদের জাহাঙ্গীর সম্পর্কে তথ্য দরকার। গত এক মাসে এই লোক কতবার ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে রক্ত নিয়েছে?
দ্রুত রেজিস্টার খাতা বের করল লোকটা। ১৩ মার্চ পাতাটা দেখে বলল, ‘স্যর, জাহাঙ্গীর তো রোগীর নাম। ঢাকা মেডিকেলের ব্লাড ক্যান্সারের রোগী। জাহাঙ্গীরের জন্য রক্ত নিয়েছে তার আত্মীয় ইদ্রিস।’
‘ওহ্,’ বলল আনোয়ার, ‘আমার ভুল হয়েছে তা হলে। আচ্ছা, ইদ্রিস গত এক মাসে ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে কতবার রক্ত নিয়েছে, জানাতে পারবেন?’
‘হ্যাঁ, অবশ্যই পারব। যারা এখানে নিয়মিত ব্লাড ডোনেট করে এবং যারা নিয়মিত রক্ত নেয়, তাদের একটা লিস্ট আমাদের কাছে আছে। দেখি সেখানে ইদ্রিসের নাম আছে কি না।’
পাতার পর পাতা উল্টাতে থাকল লোকটা। পনেরো মিনিট পর বলল, ‘হ্যাঁ, ইদ্রিস এখান থেকে নিয়মিত রক্ত নেয়। তার আত্মীয়ের জন্য প্রতি সপ্তাহে রক্ত লাগে।’
‘ইদ্রিস সম্পর্কে আমাদের সবকিছু জানান,’ বলল আনোয়ার, ‘তার মোবাইল নাম্বার, ঠিকানা-সব।’
মাথা নিচু করে বলল লোকটা, ‘স্যর, অভয় দিলে একটা কথা বলি?’
‘হ্যাঁ, বলেন।’
‘আসলে ইদ্রিস আমাদের এখানেই পার্ট-টাইম কাজ করে। আমি নিশ্চিত হতে চেয়েছিলাম এই ইদ্রিসই সেই ইদ্রিস কি না। তাই আর একবার চেক করে নিচ্ছিলাম।’
শাহেদ বলল, ‘ইদ্রিস আজ এসেছে?’
‘হ্যাঁ, এসেছে। একজন ব্লাড ডোনেট করতে এসেছে, তাকে সাহায্য করছে।’
‘আমাদেরকে সেখানে নিয়ে চলুন।
‘চলুন, স্যর।’
.
কাজ শেষ করে রুম থেকে বেরিয়ে এল ইদ্রিস। আর তখনই তাকে চেপে ধরল শাহেদ। ‘নড়ার চেষ্টা করবি না। একদম মাথায় গুলি করে দেব।’
তোতলাতে শুরু করল ইদ্রিস, ‘স্-স্যর, আ-আমি কী করেছি?’
‘চুপচাপ আমাদের সঙ্গে চল্।’
একটা মাইক্রোবাসে ইদ্রিসকে তুলে নেয়া হলো।
টেনে ইদ্রিসের গেঞ্জিটা খুলে ফেলে যা ভেবেছিল, ঠিক তা-ই দেখল আনোয়ার।
ইদ্রিসের শরীরেও সেই একই উল্কি আঁকা।
ইদ্রিসকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে শুরু করল আনোয়ার আর শাহেদ। প্রথমে মুখ না খুললেও পরে মুখ খুলতে বাধ্য হলো ইদ্রিস। ঘোলাটে বিষয়গুলো পরিষ্কার হয়ে উঠল আনোয়ার ও শাহেদের কাছে। ইদ্রিসকে নিয়ে থানার দিকে রওয়ানা হলো শাহেদ ও আনোয়ার। আরও অনেক কিছু জানার আছে তাদের। ইদ্রিসের সাহায্য দরকার।
এগারো
দুই দিন পর…
বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে আছেন রফিক সাদি। তিনি কী করবেন বুঝতে পারছেন না। নিজেকে এত অসহায় আগে কখনও লাগেনি। তাঁর মেয়ে ঝমঝম কুঠিতে বউ হয়ে গেছে, এর চেয়ে ভয়ঙ্কর আর কী হতে পারে? একটু আগে নুযহাত ফোন করেছিল। নেটওয়ার্কের জন্য কথা ভাল শোনা যাচ্ছিল না। শুধু রফিক সাদি এটুকুই বুঝলেন, নুযহাত বলছে-ভাল আছে সে। নুযহাতের এ কথা তাঁকে আশ্বস্ত করতে পারেনি। তিনি কিছু খেতে পারছেন না, মাথায় কেন জানি অসহ্য ব্যথা।
ঠিক এসময় রফিক সাদিকে জানানো হলো, তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছেন আনোয়ার নামে একজন।
মনে-মনে এই ছেলেটিকেই খুঁজছিলেন তিনি। দ্রুত উঠে দাঁড়ালেন।
ড্রয়িং রুমে রফিক সাদিকে দেখে হাসল আনোয়ার।
ছেলেটার হাসিটা খুব সুন্দর, ভাবলেন রফিক সাদি। ওই হাসি মনের ভিতর কেমন যেন একটু প্রশান্তি এনে দিল।
আনোয়ার বলল, ‘কেমন আছেন?’
সোফায় বসে চোখ বন্ধ করে রফিক সাদি বললেন, ‘আমার মেয়ে ঝমঝম কুঠিতে চলে গেছে। এই চিঠিটা রেখে গেছে।’
আনোয়ার একটু চমকে উঠল।
চিঠিটা পড়ে ঢিপঢিপ করতে থাকল বুকের ভিতরটা, কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করল না। মুখ স্বাভাবিক রেখে আনোয়ার বলল, ‘আমি জানি, সবকিছু মিলিয়ে আপনার মনে অনেক প্রশ্ন জমে গেছে। আপনার সব প্রশ্নের জবাব দিতেই এসেছি।’
‘চলো, চা খেতে-খেতে কথা বলি।’
চা এল মাত্র তিন মিনিট পর।
চায়ে চুমুক দিয়ে আনোয়ার বলল, ‘বিষয়টা একটু জটিল। কোথা থেকে শুরু করব ঠিক বুঝতে পারছি না। যা হোক, সোলেমান গাজির বাবা ইব্রাহিম গাজিকে দিয়েই শুরু করি। ইব্রাহিম গাজি একজন অপ্রকৃতিস্থ মানুষ ছিলেন। পিশাচ সাধনার প্রতি ছিল প্রবল আগ্রহ। মধ্যবয়সে এক তান্ত্রিকের কথা অনুসারে পিশাচ সাধনা শুরু করেন। এই সাধনার একটাই লক্ষ্য, পিশাচকে কাজে লাগিয়ে অভাবনীয় শক্তি অর্জন করা। ইব্রাহিম গাজি পিশাচকে নিজের মধ্যে ধারণ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। সেসময় তিনি দূর-দূরান্ত থেকে মেয়েদেরকে ধরে আনতেন। শারীরিক নির্যাতনের পর, পিশাচের উদ্দেশে বলি দিতেন তাদেরকে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি ইব্রাহিম গাজি। তখন তিনি অন্য পথ বেছে নিলেন। নিজের ছেলের মধ্যে পিশাচকে প্রবেশ করাতে চাইলেন। যৌবনে ছেলে সোলেমান গাজির মধ্যেও সাধনার বিষয়টা ঢুকিয়ে দিলেন। কিন্তু সোলেমান গাজিকেও পছন্দ করেনি পিশাচ। একসময় ইব্রাহিম গাজি মারা গেলেন। প্রবল উৎসাহে সাধনা চালিয়ে যেতে লাগলেন সোলেমান গাজি। আরও কয়েকজনকে খুঁজে বের করলেন, যারা সবাই এ অন্ধকার পথের বাসিন্দা। তাদেরকে জায়গা দিলেন এলেমদারি বনে। সোলেমান গাজির স্ত্রীও এক পিশাচ সাধক। তাই দু’জনে জমল ভাল। সিদ্ধান্ত নিলেন, তাঁদের সন্তানের জন্মের সাথে- সাথে তাকে পিশাচের উদ্দেশে বলি দেবেন। এত বড় উপহার পেয়ে পিশাচ নিশ্চয় তাঁদের কারও মধ্যে প্রবেশ করবে। জয়ের জন্মের কিছুদিন আগেই হঠাৎ সোলেমান গাজির স্বপ্নে দেখা দিল পিশাচ। সে জানাল, তাঁদের অনাগত সন্তানকে বলি দেয়ার কোনও প্রয়োজন নেই। সন্তানের বয়স যখন একুশ হবে, তখন পিশাচ তার মধ্যে প্রবেশ করবে। সোলেমান গাজির এতদিনের সাধনা যেন ঠিকানা খুঁজে পেল। পিশাচটা আরও জানাল, সে যখন জয়ের মধ্যে প্রবেশ করবে, তখন থেকে নিয়মিত তার রক্ত ও বলি চাই। এর বিনিময়ে সোলেমান গাজিকে পিশাচটা দেবে অভাবনীয় ক্ষমতা ও সম্পদ। তবে চূড়ান্ত সম্পদ আর ক্ষমতা পাওয়ার জন্য তাঁকে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হবে। জয়ের বয়স যখন একুশ, তখন ওর শরীরে প্রবেশ করল পিশাচটা। পিশাচ একবার কারও শরীরে প্রবেশ করলে সেই শরীরটা তার হয়ে যায়। তাই জয়ই পিশাচ, পিশাচই জয়। এরপর থেকে সোলেমান গাজিকে আরও বেশি সচেতন থাকতে হলো। কারণ, পিশাচকে কোনওভাবেই রাগিয়ে দেয়া চলবে না। সে রাগলে, অনর্থক জীবনহানি হবে। একে নিয়ন্ত্রণ করা কোনও সহজ বিষয় নয়। এর প্রধান খাদ্য রক্ত। আর নারীকে উৎসর্গ করলে মিলবে এর সন্তুষ্টি। সোলেমান গাজি নিয়মিত বিভিন্ন ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে রক্ত আনা শুরু করলেন। ক্লিনিকের অসৎ কর্মচারীরা এ কাজে সাহায্য করত। প্রতি সাত দিন অন্তর পিশাচের তিন ব্যাগ রক্ত প্রয়োজন হত। দু’ব্যাগ সে পান করত, আর এক ব্যাগ দিয়ে গোসল করানো হত তাকে। আর সাতচল্লিশ, ছাপান্ন বা পঁয়ষট্টি দিন অন্তর কোনও যুবতী মেয়েকে তার উদ্দেশে উৎসর্গ করা হত। এক সংখ্যাটা পিশাচের জন্য শুভ। কারণ, একের সাথে শনির একটা যোগাযোগ রয়েছে। সাতচল্লিশ সংখ্যাটির দুই অঙ্ক যোগ করলে যোগফল পাওয়া যায় এগারো, অর্থাৎ দুটো এক। ছাপান্ন এবং পঁয়ষট্টির ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার, যোগফল এগারো।’
একটু থেমে আনোয়ার আবার বলল, ‘নির্ধারিত সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও যদি কোনও যুবতী মেয়েকে পিশাচের জন্য উৎসর্গ না করা হয়, তবে সোলেমান গাজি ও তাঁর স্ত্রীর পরিণতি হবে ভয়াবহ। কারণ, তাঁদের আহ্বানেই পিশাচটা এসেছে। সোলেমান গাজি চতুর মানুষ, হিসাবে ভুল করেননি। অনুসারীদের এবং জয়কে এই কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। এরা বিভিন্ন মেয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। তারপর ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঝমঝম কুঠিতে নিয়ে এসেছে। ঝমঝম কুঠিতে আনার পর এক পর্যায়ে মেয়েগুলোর মাথা কেটে ফেলা হত। তার আগে শরীরে আঁকা হত উল্কি, আর নিয়মিত খাওয়ানো হত ভাঙের শরবত। এরপর সময়মত পিশাচের উদ্দেশে উৎসর্গ করত। উৎসর্গ প্রক্রিয়াটা বেশ অদ্ভুত। প্রথমে খোলা মাঠের মধ্যে মেয়েটাকে হাঁটু গেড়ে বসানো হত। তার ঠিক সামনে থাকত জয়, যার মধ্যে রয়েছে পিশাচটা। এরপর গলায় ইলেকট্রিক তার পেঁচিয়ে, শ্বাস বন্ধ করে মেরে ফেলা হত মেয়েটাকে। কয়েকজন তাকে চেপে ধরত, আর একজন একটা ছোট পাত্রে তার মুখের লালা সংগ্রহ করত। মেয়েটা মারা যাওয়ার পর সেই লালা জয় বা পিশাচকে দেয়া হত। আনন্দ নিয়ে এই লালা পান করত পিশাচ। এতে আরও বাড়ত তার শক্তি। এরপর মেয়েটির মৃতদেহ জয়ের পায়ের কাছে রেখে গলায় সজোরে ছুরি চালানো হত। রক্তে ভিজে যেত জয়ের পা। এতে সন্তুষ্টি বাড়ত পিশাচের। এলেমদারি জঙ্গলের কিছু জায়গায় মোগল যুগের কিছু দামি রত্ন রয়েছে। পিশাচের মাধ্যমে সেগুলো কোথায় জানতে পেরেছেন সোলেমান গাজি। ফলে দু’হাতে আসতে লাগল টাকা। সে টাকার ভাগ তিনি এলেমদারির অন্যান্য লোকদেরও দিয়েছেন।’
ঠাণ্ডা চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে আবারও বলল আনোয়ার, ‘পিশাচের মাধ্যমে সোলেমান গাজি জানতে পেরেছেন, যদি জয়ের কোনও সন্তান পৃথিবীতে আসে, তবে সে হবে প্রবল ক্ষমতাশালী। সে জয়ের সন্তান হবে না, হবে পিশাচের সন্তান। ইচ্ছা হলে সেই সন্তান সব ধ্বংস করে দিতে পারবে, আবার সব গড়তেও পারবে, পৃথিবীকে আনতে পারবে হাতের মুঠোয়। সেই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য তাঁরা নুযহাতকে বেছে নেন।’
চুপ করে শুনছেন রফিক সাদি। তাঁর দিকে চেয়ে আনোয়ার বলল, ‘আমরা ঝমঝম কুঠিতে প্রতিটা মানুষের গায়ে যে উল্কি দেখেছি, সেটা কার অবয়ব, এখন বুঝতে পারছেন?’
রফিক সাদি কাঁপা গলায় বললেন, ‘জয়ের?’
আনোয়ার একটু হেসে বলল, ‘হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। ওটা জয়ের অবয়ব।’
‘কিন্তু জয়কে আমার অফিসে দেখলাম স্বাভাবিক আর এলেমদারিতে দেখলাম অপ্রকৃতিস্থ। কারণটা কী?’
‘পিশাচটা যখন ঘুমিয়ে থাকে বা বিশ্রাম নেয়, তখন আট-দশটা স্বাভাবিক মানুষের মতই আচরণ করে জয়। কিন্তু যখন পিশাচটা সক্রিয় থাকে, তখন জয় প্রতিবন্ধীর মত আচরণ করতে থাকে।’
‘তা হলে এলেমদারির সব লোকই পিশাচের উপাসক?’
‘হ্যাঁ। এরা এলেমদারি বনে বাস করলেও কর্মসূত্রে পুরো ঢাকা শহরে ছড়িয়ে আছে। এদের কেউ ক্লিনিকে কাজ করে, কেউ অফিসে করে, কেউ দোকানের কর্মচারী। পাশাপাশি এরা শিকারের খোঁজ রাখে। বিভিন্ন মেয়ের সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে, তারপর এলেমদারি বনে নিয়ে যায়। সবসময় যে তারা সফল হয়, তা নয়, তবে চেষ্টা চলতে থাকে। আপনি ফারহানা নামে যে মেয়েটাকে ঝমঝম কুঠিতে দেখেছিলেন, তার নীরব নামে একটা ছেলের সাথে সম্পর্ক ছিল। নীরবই তাকে এলেমদারি বনে নিয়ে যায়। আর বিস্ময়কর তথ্য হচ্ছে, জয়ই কখনও নীরব, কখনও আসিফ, কখনও রফিক হয়ে নানা মেয়ের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।’
‘ফারহানা মেয়েটার কী অবস্থা এখন?’ উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করলেন রফিক সাদি।
‘আগামীকাল তাকে পিশাচের উদ্দেশে উৎসর্গ করা হবে। এটা হবে সোলেমান গাজির আটত্রিশতম শিকার। আটত্রিশতম উৎসর্গ সোলেমান গাজির পিশাচ সাধনাকে পরিপূর্ণতা দেবে। কালকের পরেই কাঙ্ক্ষিত ক্ষমতা আর সম্পদ পেয়ে যাবেন তিনি। জয়ের সন্তানকে নিয়ে তিনি পুরো পৃথিবীতে রাজত্ব করতে চান।’
রফিক সাদি ভাঙা গলায় বললেন, ‘আমার মেয়ে তো জয়ের সন্তান গর্ভে ধারণ করেছে, তা হলে ওটা কি পিশাচের সন্তান?’
‘হ্যাঁ, ওটা পিশাচ এবং নুযহাতের সন্তান।’
‘এখন আমরা কী করব?’
‘সোলেমান গাজিকে সফল হতে দেয়া যাবে না। কালকে রাতে যদি আটত্রিশতম উৎসর্গ করতে পারেন, তা হলে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবেন তিনি। তাঁকে ধরার মত সব প্রমাণ আমাদের হাতে আছে। আমি প্রস্তুত, পুলিশও প্রস্তুত।’
‘তোমার পরিকল্পনা কী?’
‘কালকে পিশাচটাকে রাগিয়ে দিলে সে সর্বনাশ করবে জয়, সোলেমান গাজি ও তাঁর স্ত্রীর। এতদিনের সাধনা একদিনেই শেষ হয়ে যেতে পারে। পিশাচ প্ৰথমে এই তিনজনের প্রাণ নেবে। তারপর চিরদিনের মত চলে যাবে। আর আগে থেকেই পুলিশ এলেমদারি বনের বিভিন্ন জায়গায় উপস্থিত থাকবে, সময়মত সবাইকে গ্রেফতার করবে তারা।’
‘আমার মেয়েটা কি মারা যাবে, বাবা?’ প্রায় কেঁদে ফেললেন রফিক সাদি।
‘আপনি শান্ত হোন। চিন্তা করবেন না। আশা করি, নুযহাত আর ফারহানাকে আমরা বাঁচাতে পারব। আর নুযহাতকে তো ওঁরা কোনওভাবেই মারবেন না। কারণ, নুযহাতের গর্ভে জয়ের সন্তান। জয় নুযহাতকে নানাভাবে সম্মোহিত করেছে। ওর হাতে যে তাবিজ আছে, সেগুলো যেভাবে হোক সরাতে হবে। তাবিজের মাধ্যমেই জয় নুযহাতকে নানা নির্দেশনা পাঠাত।’
নিজেকে একটু স্বাভাবিক করার চেষ্টা করে রফিক সাদি বললেন, ‘তুমি এত কিছু কীভাবে জানলে?’
‘পিশাচ সাধনা বিষয়ে আমার আগে থেকেই ধারণা রয়েছে। প্রচুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও ছিল। আর সোলেমান গাজির কাছের সহযোগী ইদ্রিসকে আমরা ধরতে পেরেছি। তার মাধ্যমে আমরা প্রচুর তথ্য পেয়েছি। সোলেমান গাজি যে সাঁইত্রিশজন মেয়েকে হত্যা করেছে, তাদের পরিচয়ও জানতে পেরেছি। বাড়ির পিছনের কবরস্থানে কবর দেয়া হয়েছিল তাদেরকে। আপনাকে এই ধরনের অন্য একটা ঘটনা বলি। উনিশ শ’ সাতানব্বুই সালে ইন্দোনেশিয়ায় পুলিশ আহমাদ সুবাদজি নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছিল। সেই লোকও পিশাচ সাধক ছিল। বিভিন্ন নারীকে ধরে ইলেকট্রিক তার পেঁচিয়ে হত্যা করত। এরপর পান করত তাদের লালা। এরপর বাড়ির সামনেই কবর দিত লাশগুলোর। তবে আসলেই পিশাচ তার ওপর ভর করেছিল কি না, সে ব্যাপারে অবশ্য নিশ্চিত হওয়া যায়নি পরবর্তীতে ইন্দোনেশিয়ার আদালত লোকটাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। আসলে সোলেমান গাজির মত এমন ভয়ঙ্কর লোক সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে।’
‘আমি আর এসব কিছু শুনতে চাই না, আমার মেয়েকে তুমি বাঁচাও।’
‘আপনাকে এবং ড্রাইভার মহসিনকে কালকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। মহসিন এলেমদারি বনের বাইরে থাকবে। আপনি আর আমি ভেতরে যাব। আপনি সুযোগ বুঝে ফারহানা আর নুযহাতকে নিয়ে পালাবেন। এরপর সোজা ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেবেন।’
‘আর তুমি?’
‘প্রথমে নিজে, এরপর আমার বন্ধু শাহেদকে নিয়ে বাকিটা সামলাব। চিন্তার কিছু নেই।’
‘কিন্তু আমরা ওদের ওখানে যাব কীভাবে? মানে উৎসর্গের সময় ওরা আমাদেরকে দেখলে কিছু বলবে না?’
‘আমরা ওদের একজন হয়েই যাব। প্রতি উৎসর্গের সময় এলেমদারির বাসিন্দারা কালো জোব্বার মত পোশাক পরে, নাক-মুখ ঢাকা থাকে কালো কাপড়ে। এ ব্যাপারে আমাদেরকে সাহায্য করছে ইদ্রিস। তার কাছ থেকে এমন দুটো পোশাক জোগাড় করেছি। ওই দুটো পরেই কালকে আমরা এলেমদারি বনে যাব। প্রস্তুত থাকবেন। দুপুরের দিকে রওনা দেব আমরা।’
‘অবশ্যই প্রস্তুত থাকব,’ বললেন রফিক সাদি
‘ব্যাগে আপনার জন্য পোশাক নিয়ে এসেছি। একটু ঢিলাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে দর্জির দোকান থেকে আজই ঠিক করিয়ে নেবেন।’
‘ঠিক আছে।’
আনোয়ার উঠে দাঁড়াল। তারও দরকার ব্যাপক প্রস্তুতি।
বারো
কালো জোব্বা পরেছে আনোয়ার আর রফিক সাদি। মুখ ঢাকা কালো কাপড়ে। শাহেদের দিকে তাকিয়ে আনোয়ার বলল, ‘রফিক সাহেব আর আমি বনে ঢুকছি। এখন রাত এগারোটা। ওদের মূল অনুষ্ঠান শুরু হবে বারোটার পর। ইদ্রিসের মাধ্যমে যে শর্টকাট পথের কথা জানতে পেরেছি, ওই পথেই যাব। এরপর ঝমঝম কুঠির কাছে গিয়ে দূর থেকে লক্ষ রাখব ওদের ওপর। সুযোগ বুঝে মিশে যাব ওদের দলের সাথে।’
‘একবারে পুলিশ ফোর্স নিয়ে ওখানে অভিযান চালালে ভাল হত না?’ বলল শাহেদ।
‘পিশাচের মোকাবেলা করার নিয়ম পুলিশ জানবে না। মিস্টার সাদি আর আমার লাইসেন্স করা অস্ত্র সাথে রাখছি। তোর ফোর্সের লোকজন এলেমদারি বনের নানান জায়গায় রাখ। গুলির শব্দ পেলেই অ্যাকশনে যাবি, তার আগে নয়।’
‘ঠিক আছে। তোর ওপর আমার ভরসা আছে। জানি, অনর্থক ঝুঁকি নিবি না।’
‘চিন্তা করিস না।’
দেরি না করে রফিক সাদি ও আনোয়ার ঢুকে পড়লেন এলেমদারি বনে। বনের বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নিল শাহেদ চৌধুরীর ফোর্স। বনের বাইরে হাইওয়েতে গাড়িতে অপেক্ষা করছে মহসিন।
.
অন্ধকারে ছোট একটা টর্চ জ্বেলে নতুন এক পথ ধরে ঝমঝম কুঠির দিকে যাচ্ছেন রফিক সাদি ও আনোয়ার। ঝমঝম কুঠিতে সৌরবিদ্যুৎ রয়েছে, তাই আশপাশটা বেশ আলোকিত। ঘন গাছপালা এড়িয়ে এগোতে হচ্ছে, কাজটা যথেষ্ট কঠিন। রাতের পোকামাকড় হুট করে বেয়ে উঠছে তাঁদের শরীরে। ক্ষতবিক্ষত করে ফেলল এক কাঁটাযুক্ত গাছ, তবুও দাঁতে দাঁত চেপে তা সহ্য করল আনোয়ার, বুঝতে দিল না রফিক সাদিকে।
আনোয়ার পুরোপুরি নির্লিপ্ত হলেও বেশ ভয় লাগছে রফিক সাদির। কেন জানি মনে হচ্ছে, মেয়েকে নিয়ে ঘরে ফেরা হবে না।
.
ঝমঝম কুঠি থেকে খানিক দূরে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে আনোয়ার ও রফিক সাদি। আশপাশে টের পাওয়া যাচ্ছে বেশ চাঞ্চল্য। হঠাৎ ওরা দেখল, দল বেঁধে হেঁটে যাচ্ছে কালো কাপড় পরা একদল মানুষ। বিড়বিড় করে মন্ত্রের মত কিছু বলছে।
চাপা গলায় বলল আনোয়ার, ‘দেরি না করে ওদের পিছনে জুটে যাব আমরাও। কোনও কথা বলবেন না। কোনও কিছু করার দরকার নেই। তবে আমি ইঙ্গিত করলে প্রথম সুযোগেই ফারহানা আর নুযহাতকে নিয়ে পালিয়ে যাবেন। বুঝতে পেরেছেন?
মাথা নাড়লেন রফিক সাদি।
দলের পিছনে হাঁটতে লাগল দু’জন।
পিছনে পড়ল ঝমঝম কুঠি। কবরস্থানকে পাশ কাটিয়ে ওরা গিয়ে দাঁড়াল মাঠে। আগে থেকেই অপেক্ষা করছেন সোলেমান গাজি। জ্বলছে বিশাল আগুন। সবার হাতে-হাতে তুলে দেয়া হচ্ছে ভাঙের শরবত। ছোট মঞ্চে দাঁড়িয়ে সোলেমান গাজি। আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে জয়, পাশে নুযহাত। ওর চোখ বন্ধ। কোথায় আছে বোধহয় জানে না, জানতেও চায় না। হাঁটু গেড়ে বসে আছে ফারহানা, থরথর করে কাঁপছে তার শরীর। অপেক্ষা করছে মৃত্যুর জন্য। ভাল করেই জানে, উৎসর্গ করা হবে তাকে।
কয়েক ব্যাগ রক্ত হাতে অপেক্ষা করছে একজন, ইঙ্গিত পেলেই ঢেলে দেবে পিশাচের মুখে।
এসব রক্ত মেটাবে পিশাচের পিপাসা। সে আরও পান করবে আটত্রিশতম মেয়ের লালা। এরপর বেচারীর তাজা রক্তে ভিজিয়ে নেবে পা। এতদিনের সাধনা সার্থক হবে সোলেমান গাজির। কিন্তু কোনওভাবেই পিশাচকে রাগিয়ে দিলে চলবে না, সেক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে সোলেমান গাজির জীবনে 1
ছোট মঞ্চের ওপর সংস্কৃত ভাষার মন্ত্র পাঠ শুরু করলেন সোলেমান গাজি। তা শুনে যেন সজাগ হলো জয়। মুখে ফুটল ভয়ঙ্কর হাসি। বুঝে গেছে, একটু পরেই খাবার হিসাবে আসছে মেয়েদের লালা, ভিজবে রক্তে পা।
গম্ভীর কণ্ঠে বলল জয়নাল, ‘আহ্! মানুষের রক্ত! পিশাচ শ্রেষ্ঠ, মানুষ নির্বোধ।’
চারদিক ভরে উঠেছে ধূপের গন্ধে। অপার্থিব এক পরিবেশ। মন্ত্রের তালে- তালে দুলছে কালো কাপড় পরা মানুষ। বারবার স্পর্শ করছে শরীরের উল্কি তারাও ক্ষমতা ও সম্পদ চায়। জয়ের পুরো শরীরে কিছু ঘটছে, মুখ থেকে বেরোচ্ছে হিংস্র জন্তুর মত শব্দ।
হঠাৎ সোলেমান গাজি ইঙ্গিত করলেন পিশাচের মুখে রক্ত ঢালতে।
দ্রুত এগিয়ে গেল আনোয়ার, চোখের নিমিষে লোকটির হাত থেকে কেড়ে নিল রক্তের ব্যাগদুটো।
ঘটনার আকস্মিকতায় ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে তাকিয়ে থাকল লোকটি।
সবার চোখের সামনেই রক্তের ব্যাগগুলো ফুটো করে বহুদূরে ছুঁড়ে দিল আনোয়ার। যেন আগুন বেরোতে থাকল পিশাচটার চোখ থেকে। লোহার মত শক্ত হয়ে উঠল মুখের মাংসপেশি। রেগে উঠেছে হঠাৎ করেই!
চেঁচিয়ে উঠলেন সোলেমান গাজি, ‘কী হচ্ছে এখানে? অ্যাই, ওই নির্বোধটাকে কেউ ধর! আজ ওর রক্তেই তাঁর পিপাসা মিটবে।’
পকেট থেকে রিভলভারটা বের করল আনোয়ার, ধমকে উঠল, ‘খবরদার! কেউ কাছে আসবে না! একদম শেষ করে দেব!’
একদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে আছে সবাই, কিন্তু এগোবার সাহস নেই কারও।
হঠাৎ চোখ মেলে তাকাল নুযহাত, উঠে দাঁড়িয়েছে ফারহানাও। পিপাসায় ছটফট করছে জয়। রফিক সাদির দিকে ইঙ্গিত করল আনোয়ার, পরক্ষণে আকাশে গুলি করল।
নুযহাত ও ফারহানার পিছনে এসে থেমেছেন রফিক সাদি। মাথাটা কালো কাপড় দিয়ে ঢাকা বলে তাঁকে আলাদা করতে পারেনি কেউ। ছুরি দিয়ে কেটে দিলেন নুযহাতের হাতের তাবিজ। খুব কাছে গিয়ে কী যেন বললেন তিনি নুযহাত ও ফারহানাকে।
ঘোরটা কেটে গেছে নুযহাতের। একই অবস্থা ফারহানার। পিছাতে শুরু করেছে ওরা তিনজন।
সবার নজর আনোয়ারের ওপর। কারও খেয়াল নেই নুযহাত এবং ফারহানার দিকে। সুযোগ বুঝে ওরা সরে যেতে শুরু করেছে।
গুলির শব্দ পৌঁছে গেছে শাহেদ চৌধুরীর কানে, কিছুক্ষণের ভিতর এখানে চলে আসবে পুলিশ। চিৎকার করে বলল আনোয়ার, ‘বাঁচতে হলে সবাই পালাও! পুলিশ আসছে!’
দূরে শোনা গেল পুলিশের বাঁশির শব্দ।
পিশাচ সাধক হলে কী হবে, লোকগুলো এক-একটা কাপুরুষ। সবাই নানান দিকে দৌড় দিল, ভাবছে পালিয়ে যেতে পারবে জঙ্গলে।
এই সুযোগে মহাসড়কের দিকে ছুটলেন রফিক সাদি, নুযহাত ও ফারহানা। মাত্র এক মিনিট পেরোবার আগেই মাঠে থাকলেন শুধু সোলেমান গাজি, তাঁর স্ত্রী, জয়ের শরীরধারী পিশাচ ও আনোয়ার।
মন্ত্রপাঠ চালিয়ে পিশাচকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন সোলেমান গাজি। মঞ্চে উঠে রিভলভারের বাঁট দিয়ে সোলেমান গাজির মাথায় জোর এক গুঁতো বসিয়ে দিল আনোয়ার। মন্ত্রপাঠ থেমে গেল সোলেমান গাজির।
সংস্কৃত ভাষার কিছু দরকারি মন্ত্র আনোয়ারের মুখস্থ। পকেট থেকে বের করে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে দিল বেলি ফুলের মালা। এই ফুল পছন্দ নয় পিশাচের। জোরে-জোরে মন্ত্রপাঠ শুরু করল আনোয়ার।
এতে অনিয়ন্ত্রিতভাবে থরথর করে কাঁপতে লাগল জয়ের শরীর। দু’হাত দু’দিকে ছড়িয়ে চিৎকার করে উঠল পিশাচ। সহ্য করতে পারছে না, তার চাই রক্ত। এদিকে আনোয়ারের মন্ত্র সৃষ্টি করছে তার শরীরে যন্ত্রণা।
সোলেমান গাজির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পিশাচ। বড়-বড় নখ গেঁথে গেল সোলেমান গাজির পেটের মধ্যে।
ভয়ানক ব্যথা পেয়ে বিকট এক আর্তনাদ ছাড়লেন সোলেমান গাজি। ধড়াস্ করে পড়লেন মঞ্চের মেঝেতে। এদিকে তাঁর স্ত্রী বেগতিক বুঝে ছুট দিলেন বেসামাল হরিণীর গতি তুলে। খেয়ালই নেই, পিশাচটা ক্ষতবিক্ষত করছে তাঁর স্বামীর দেহ।
পিশাচকে ডেকে এনে সন্তুষ্ট করতে পারেননি সোলেমান গাজি, তাই আজ নিস্তার নেই তাঁর। জোরালো আওয়াজ তুলে লোকটার ঘাড়টা ভেঙে দিল পিশাচ। বড়-বড় নখ দিয়ে টেনে বের করতে লাগল হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ও পাকস্থলি। পিপাসা মিটিয়ে নিতে হবে শত্রুর রক্তে। কিন্তু চোঁ-চোঁ করে কয়েক লিটার রক্ত চুষে নিয়েই তার চোখ পড়ল আনোয়ারের ওপর। মন্ত্রপাঠ শেষ করেছে ওই শত্রু, স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে চলে যেতে হবে পিশাচকে।
কিন্তু আনোয়ারকে খতম না করে যাওয়ার ইচ্ছা নেই পিশাচটার। ভয়ঙ্কর রাগ তার। তাড়ানোর জন্য মন্ত্র পড়ছে নির্বোধ মানুষ! ওই লোক কি জানে না, আসলে সে কী করতে পারে!
শত্রুর দিকে এগোতে শুরু করল পিশাচ, কিন্তু এক পা-ও পিছিয়ে গেল না আনোয়ার। পালানোর চেষ্টাও করল না। পিশাচের চোখে চোখ রেখে এগোতে লাগল। বলল, ‘চলে যাও! চলে যাও! তোমাকে উপাসনার কেউ নেই, মানুষ নিজেই ক্ষমতাশালী, তার দরকার নেই পিশাচের ক্ষমতা!’
এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল পিশাচ। আশ্চর্য, এই মানুষটা তাকে ভয় পাচ্ছে না, উল্টো তারই কেমন ভয়-ভয় লাগছে!
আনোয়ার চিৎকার করে আবারও পড়তে শুরু করেছে সংস্কৃত মন্ত্ৰ।
গুরুগম্ভীর ওই মন্ত্র শুনতে শুরু করে হঠাৎ করেই থমকে দাঁড়াল পিশাচটা। টের পেল, আর এগোতে পারছে না সে।
অদৃশ্য কোনও শুভ শক্তিতে যেন বলীয়ান আনোয়ার। পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বলল: ‘তুমি আর এগোবে না! একটু এগোলেই ধ্বংস তোমার সুনিশ্চিত! হাঁটু গেড়ে বসো! পরাজয় স্বীকার করো মানুষের কাছে!’
এদিকে কুচকুচে কালো মেঘে ঢেকে গেছে আকাশ। হঠাৎ করেই চারপাশে শুরু হলো দমকা, ঝোড়ো বাতাস। মেঘে নীলচে আলো এঁকে-বেঁকে ঝলসে উঠল, পরক্ষণে কড়-কড়াৎ আওয়াজে কাছেই নামল বাজ। বাতাসের ঝটকা লেগে আনোয়ারের মনে হলো, যেন সামান্য পাতার মত উড়ে যাবে সে। কেউ যেন ক্রমাগত হামলা করতে চাইছে, কিন্তু কোথায় যেন বাধা। ডান থেকে বামে, বাম থেকে ডানে সরে গিয়ে যেন আসতে চাইছে আনোয়ারের ক্ষতি করতে!
দৃঢ় কণ্ঠে বলল আনোয়ার, ‘হাঁটু গেড়ে বসো! পরাজয় স্বীকার করো! মানুষই শ্রেষ্ঠ!’ আনোয়ার কথাটা মাত্র বলেছে, এমন সময় হঠাৎ কী যেন একেবারে বিদ্যুতের গতিতে লাগল পিশাচের বুকে। বিকট হাহাকার করে উঠল পিশাচটা। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল মঞ্চে।
সারা শরীর ঘেমে যাচ্ছে আনোয়ারের। চোখ বন্ধ করে আবারও বলল, ‘নতি স্বীকার করো! হাঁটু গেড়ে বসো! তোমার উপাসনার জন্য কেউ নেই, কেউ নেই…চলে যাও…চলে যাও…’
কত সময় পেরিয়ে গেছে আনোয়ার জানে না। হঠাৎ চোখ মেলে দেখল, হাঁটু গেড়ে বসে আছে জয়। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে জল।
আনোয়ার জানে, নির্বোধ এই প্রাণীটাকে আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এখন উপাসনা করলেও আসবে না ওই ভয়ঙ্কর পিশাচ।
পুলিশ ফোর্স নিয়ে চলে এসেছে শাহেদ চৌধুরী।
আনোয়ার জয়কে স্পর্শ করতেই লুটিয়ে পড়ল তার দেহ।
চলে গেছে পিশাচটা, কিন্তু যাওয়ার আগে নিয়ে গেছে জয়ের প্রাণটা। হঠাৎ এলেমদারি বনে শোনা গেল পোকামাকড়ের স্বাভাবিক শব্দ। বনের ঘোলাটে অন্ধকারটা কেটে গেছে।
শাহেদ চৌধুরীর দলের পুলিশ-সদস্যরা গ্রেফতার করেছে সোলেমান গাজির বেশিরভাগ সঙ্গীদেরকে। কিন্তু পালিয়ে গেছেন সোলেমান গাজির স্ত্রী।
কিছুক্ষণ পর নুযহাত ও ফারহানাকে নিয়ে ঢাকার পথে রওয়ানা দিলেন রফিক সাদি।
তেরো
দুই মাস পর…
রফিক সাদির ফোন পেয়ে হাসপাতালে ছুটে গেল আনোয়ার। প্রসব বেদনা উঠেছে নুযহাতের। ঝমঝম কুঠি থেকে ফিরেই বাচ্চাটা নষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন রফিক সাদি। কিন্তু ডাক্তার বলেছেন, এখন বাচ্চা নষ্ট করতে চাইলে মায়ের ক্ষতি হবে, মারাও যেতে পারে রোগিণী। আনোয়ারের হাত ধরে বললেন রফিক সাদি, ‘এখন কী হবে? এই সন্তান জন্ম নিলে বহু মানুষের ক্ষতি করবে। ও তো পিশাচের সন্তান।’
মুখে হাত বুলাতে-বুলাতে বলল আনোয়ার, ‘শুধু পিশাচের সন্তান নয়, নুযহাতেরও সন্তান।’
‘মানে?’
‘এই বাচ্চাটার মধ্যে মানুষ সত্তা বা পিশাচ সত্তা দুটোই থাকবে।’
‘কী বলতে চাও তুমি?’
‘যদি বাচ্চাটাকে খুব ভাল পরিবেশ দেয়া যায়, হয়তো কখনও তার পিশাচ সত্তা বেরোবে না। কিন্তু ….
‘কিন্তু কী?’
‘তার যে অভাবনীয় ক্ষমতা রয়েছে, তা চিরকাল গোপনও রাখা যাবে না। একসময় সে জানবে সবই। যেমন ধরুন, যখন সে রাগ করবে, তখন হয়তো দূর থেকেই কাউকে শাস্তি দিতে পারবে, কাউকে দূর থেকে সম্মোহিত করতে পারবে। এসব আবিষ্কার করার পরে নিয়মিত এগুলোর চর্চা করবে। আর চর্চার ফলে তার ক্ষমতাও বাড়তে থাকবে।’
‘আমি এত ঝামেলা চাই না। জন্মের পরেই একে মেরে ফেলতে হবে।’
‘কিন্তু একটু চেষ্টা করলে হয় না? প্রবল চেষ্টা করলে হয়তো কোনও দিনও তার পিশাচ সত্তাটা জেগে উঠবে না।’
‘আমি কোনও চেষ্টা করতে চাই না। ধরে নিলাম বাচ্চাটা মানুষের মতই বেড়ে উঠল। কিন্তু কী পরিচয়ে তাকে আমি মানুষ করব?’
আনোয়ার চুপ করে রইল।
রফিক সাদি নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, ‘আমি আমার মেয়েকে নিয়ে দেশের বাইরে চলে যাব। ঝমঝম কুঠি থেকে ফেরত আসার পরেই নুযহাত মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে, তাই তাকে সুস্থ করতে হবে। এই আবর্জনাকে কোনও অবস্থাতেই গ্রহণ করব না।’
‘তা হলে কী করতে চান?’
‘আমার অনুরোধ, তুমি একে মেরে ফেলবে।’
‘আমি? মেরে ফেলব! কী বলছেন এসব!’ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল আনোয়ার।
‘হ্যাঁ, বাবা, প্লিজ, এতে না বোলো না। তুমি আমার মেয়ের জন্য এত কিছু করেছ, এই শেষ উপকারটুকু করো। হাতজোড় করে তোমার কাছে অনুরোধ করছি,’ ধরা গলায় বললেন রফিক সাদি।
দুর্বলভাবে মাথা নাড়ল আনোয়ার।
যথাসময়ে স্বাভাবিক ডেলিভারির মাধ্যমে নুযহাতের ফুটফুটে ছেলে হলো। দেখতে কী সুন্দর, চোখ ফেরানো যায় না। টানা-টানা চোখ, গোলাপি ঠোঁট আর ধবধবে সাদা গায়ের রং।
রফিক সাদি এক মুহূর্ত দেরি না করে বাচ্চাটাকে আনোয়ারের কোলে তুলে দিলেন। বললেন, ‘কাল সকালেই নুযহাতকে এখান থেকে নিয়ে যাব। ভিসা- পাসপোর্ট রেডি। দশ দিন পর কানাডা চলে যাচ্ছি আমরা। ওখানে আমার বড় ভাই থাকেন। নুযহাতকে আর দেশে ফিরতে দেব না, কিন্তু হয়তো একসময় ফিরব আমি। তুমি এই আবর্জনাটাকে আজ রাতেই শেষ করে দাও। এটা নুযহাতের নয়, পিশাচের সন্তান।’
আনোয়ারের পকেটে দশ লাখ টাকার চেক গুঁজে দিলেন রফিক সাদি, তারপর বললেন, ‘প্লিজ, রাখো এটা, কোনও প্রতিদান হিসেবে নেবে না। তুমি যা করেছ, তার প্রতিদান শুধু জীবন দিয়েই দেয়া যায়। এই টাকা এক কৃতজ্ঞ বাবার উপহার। নুযহাত যেমন আমার সন্তান, তেমনি তুমিও আমার সন্তান।
আর মানা করল না আনোয়ার।
বাচ্চাটাকে ভালভাবে তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে চুপিচুপি ক্লিনিক থেকে বেরিয়ে এল আনোয়ার। ওখানে সিসিটিভি ক্যামেরা নেই, তাই ভয়েরও কারণ নেই। বাচ্চাটার জন্ম হয়েছে মাত্র কয়েক ঘণ্টা, এখনই চারদিকে তাকাচ্ছে। আনোয়ারের শরীরের সঙ্গে লেগে আছে সে। মনে হচ্ছে আনোয়ারই তার সবচেয়ে আপন। এত ছোট বাচ্চা এর আগে কোলে নেয়নি ও। বাচ্চাদের শরীরে এত সুন্দর ঘ্রাণ থাকে, তা ও আগে জানত না। আনোয়ার ভাবছে, বাচ্চাটাকে নিয়ে কী করবে। কোনও নদী বা খালে ফেলে দেবে? নাকি রাস্তায় ফেলে রাখবে?
কিন্তু মনের অন্য এক অংশ আনোয়ারকে কঠোর সুরে বলল, এটা মানুষের বাচ্চা, মানুষ হয়ে মানুষকে হত্যা করলে নরকেও স্থান হবে না হত্যাকারীর। সত্যি যদি এই বাচ্চা একসময় ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে, তখন দেখা যাবে। কোনও ধারণার ওপর ভিত্তি করে কোনও বাচ্চাকে কখনোই হত্যা করা যায় না।
বাচ্চাটাকে হত্যা করতে পারল না আনোয়ার, রাতে রাখল এক এতিমখানার বারান্দায়। কে জানে, হয়তো ওখানেই মারা যাবে বাচ্চাটা, কিংবা হয়তো তাকে কোলে তুলে নেবে কেউ।
মনে-মনে স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা করল আনোয়ার: ‘হে, পরম করুণাময়, এই বাচ্চা যেন চিরকাল মানুষ হিসাবেই বেড়ে ওঠে। তুমি তাকে করুণা করো। তার খারাপ সত্তাটা যেন কখনও জেগে না ওঠে।’
কেন যেন খুব কষ্ট হচ্ছে ওর, চোখে চলে এল জল। আরেকবার বাচ্চাটাকে দেখে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাঁটতে লাগল নিজ বাড়ির উদ্দেশে।
চোদ্দ
ছয় বছর পর…
রাতটা একটু অন্যরকম। অনেক আলোতেও সবকিছু কেমন আবছা, দূরের পৃথিবীকে মনে হচ্ছে অপার্থিব জগতের দৃশ্য। চোখটা কেন জানি বিশ্রাম চাইছে, কিছু দেখতেও যেন কষ্ট।
রাস্তায় জ্বলছে টিমটিমে আলো। কিছু সময় পর পর তীব্র গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে দুই-একটা গাড়ি। বেশ কিছুক্ষণ ধরে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে। আজ তার বাসায় যাওয়ার তাড়া নেই। ভাল লাগছে একা-একা হাঁটতে। আবার কেন জানি হচ্ছে অজানা এক আশংকা। পথ আগলে দাঁড়িয়েছে কয়েকটা কুকুর। চাপা স্বরে চিৎকার করছে তারা। হাতের নড়াচড়া এবং মুখের শব্দেও পালিয়ে গেল না। লক্ষ্যে অবিচল, সামনে এগোতে দেবে না মানুষটাকে। কিন্তু ভয় পেল না সে। দেখাই যাক কী করতে চায় কুকুরগুলো। বোঝা যাচ্ছে ইচ্ছা নেই কামড়ানোর। একটা কুকুর মুখ দিয়ে ঠেলতে লাগল তাকে। সামনে এগোতে লাগল আরও দুটো। এমন একটা ভাব, যেন কোনও নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যেতে চাইছে। কুকুরগুলোর ইচ্ছার কাছে নিজেকে সঁপে দিল সে। বড় রাস্তা বাদ দিয়ে ছোট এক গলিতে ঢুকল কুকুরগুলো। ওদের পিছে যেতে লাগল মানুষটাও।
একটা গলি পেরিয়ে ছোট রাস্তা পাওয়া গেল। এখানে দেখা যাচ্ছে ক’জন মানুষ। রাস্তার পাশে চায়ের দোকানে গল্প করছে কেউ। যানবাহনের ভিড়ও এখানে একটু বেশি। হঠাৎ আনোয়ার নামের সেই মানুষটা লক্ষ করল, রাস্তার পাশে ভিক্ষা করছে এক মহিলা। তার সামনে শুয়ে আছে একজন মানুষ। একটা সাদা চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে তাকে। সেদিকে এগিয়ে গেল কুকুরগুলো। তাই করল আনোয়ারও। ওকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে বলল মহিলা, ‘ভাই গো! আমার বাচ্চাড়া মইরা গেছে। দাফন-কাফনের টাকা নাই। কিছু সাহায্য করেন।’
মনটাই খারাপ হয়ে গেল আনোয়ারের। প্রথমে ভেবেছিল, ঘুমিয়ে আছে কেউ, এখন বোঝা যাচ্ছে, মারা গেছে। শরীরে কোনও নড়াচড়া নেই, নিঃশ্বাস- প্রশ্বাসের কোনও চিহ্নও নেই। আনোয়ার পকেট থেকে এক শ’ টাকার একটা নোট মহিলার দিকে এগিয়ে দিল। কান্না থামিয়ে টাকাটা হাতে নিল মহিলা। কৃতজ্ঞতার ছায়া পড়ল মুখে। বলল, ‘আল্লাহ আপনার ভাল করুন।’
আনোয়ার ভাবল, একটু কথা বলা যাক মহিলার সাথে।
‘আপনি থাকেন কোথায়?’
‘এই তো, একটু সামনের বস্তিতে।’
‘আপনার স্বামী কোথায়?’
‘উনি বাসাতে।’
‘কী করেন আপনার স্বামী?’
‘রমনা পার্কে চা-সিগারেট বিক্রি করে।’
‘আপনার ছেলে মারা গেছে কখন?’
মহিলা উত্তর দেয়ার আগেই সবাইকে চমকে দিয়ে চাদর সরিয়ে উঠে বসল ছেলেটা। তেমন অবাক হয়নি আনোয়ার। বুঝতে পেরেছে পুরোটাই এই মহিলার ভণ্ডামি। নিজের ছেলেকে মৃত সাজিয়ে ফায়দা লোটার চেষ্টা। মহিলাকে কঠিন এক ধমক দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল আনোয়ার, তখন দেখতে পেল ফ্যাকাসে হয়ে গেছে মহিলার মুখ। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে তার। দ্রুত উঠে দাঁড়াল। মহিলার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বাচ্চা ছেলেটা। এখন লক্ষ করা যাচ্ছে তার বুকের ওঠা-নামা।
আনোয়ার বলল, ‘কী উঠে দাঁড়ালে কেন? নিজের বাচ্চাকে মৃত সাজিয়ে ব্যবসা? দাঁড়াও, তোমাকে পুলিশে দেব।’
বাচ্চা ছেলেটাও ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়াল। তার মধ্যে তেমন কোনও ভাবান্তর নেই।
আনোয়ারের দিকে তাকিয়ে বলল মহিলা, ‘এ হতে পারে না! পারে না!’ বলতে-বলতে সজোরে দৌড় দিল সে। একজন মহিলা এত জোরে দৌড়াতে পারে জানা ছিল না আনোয়ারের।
আশপাশে আরও কিছু মানুষ এগিয়ে এসেছে। তারা আনোয়ারকে বলতে লাগল, ‘এই মহিলা গত কয়েক ঘণ্টা ধরে ছেলের লাশ নিয়ে এখানে বসে আছে। অনেকেই সাহায্য করেছে। আসলে সব প্রতারণা। মা-ছেলে মিলে ভাল ব্যবসা শুরু করছে।’
উৎসুক এক লোক বলল বাচ্চাটাকে পুলিশে দিতে। ছোটবেলা থেকেই ঠক- বাটপারি শিখেছে।
আরেকজন বলল, ‘না। পুলিশে দিলে কাজ হবে না। আমরাই দু’-এক ঘা বসিয়ে দিই।’
আরও কয়েকজন তাকে সমর্থন জানাল।
সবাইকে শান্ত করতে চাইল আনোয়ার। যাকে ঘিরে এত উত্তেজনা সে একেবারে নীরব। আনোয়ার বলল, ‘এই, ছেলে, তোমার বাড়ি কোথায়?’
ছেলেটা কিছু বলল না।
আরেকজন মুখ খুলল, ‘ওই, ঠিকঠাক বল, তোর বাড়ি কোথায়?’
ছেলেটা অস্ফুট স্বরে বলল, ‘জানি না।’
নানা প্রশ্নবাণে তাকে জর্জরিত করা হলেও একই উত্তর দিল সে: জানি না।
রাত হয়েছে। আরও কিছুক্ষণ পর ভিড় হালকা হবে, ভেবেছিল আনোয়ার। কিন্তু উৎসাহ হারিয়ে বিদায় নিল না বেশিরভাগ মানুষ। নানান মন্তব্য করছে।
আনোয়ার ভেবেছিল, বাড়ি ফিরবে। তারপর মনে হলো, কে জানে, বাচ্চাটা হয়তো তার বাসা চেনে না। একে দেখে পথশিশু বলেও মনে হচ্ছে না। যেন কোনও সচ্ছল পরিবারের সন্তান। যদিও কাদামাটি মেখে আছে শরীরে, পরনে ছেঁড়া প্যান্ট ছাড়া কিছুই নেই, তবুও চেহারার মধ্যে কেমন এক আভিজাত্যের ভাব।
‘আপনারা ভিড় করবেন না, আমি ওকে থানায় নিচ্ছি, ভিড় করা লোকগুলোকে বলল আনোয়ার। ওর দাপটের ভঙ্গি দেখে সবাই ধরে নিল, ও নিজেই আসলে পুলিশের বড় অফিসার।
কয়েকজন চামচার মত সায় দিল ওর কথায়।
কেউ আপত্তি করছে না দেখে ছেলেটার হাত ধরে হাঁটতে শুরু করে ওই জায়গা থেকে সরে এল আনোয়ার। অনেকটা দূরে এসে বলল, ‘তুমি এখন কী করবে?’
‘আপনার সাথে যাব।’ স্পষ্ট এবং শুদ্ধ উচ্চারণ ছেলেটির।
‘আমার সাথে যাবে?!’
‘হ্যাঁ।’
‘যে মহিলাকে দেখলাম, সে কি তোমার মা?’
ছেলেটা উত্তর দিল না। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল দূরে।
‘আমার সাথে কোথায় যাবে তুমি?’ আবার জিজ্ঞেস করল আনোয়ার।
‘আপনার বাসায় যাব।’
‘এটা সম্ভব নয়। তুমি ঠিকানা বলো, বা তোমার মা-বাবার কারও মোবাইল নাম্বার থাকলে বলো। আমি তোমাকে পৌছে দেব।’
ছেলেটা কাঁদতে লাগল।
আনোয়ারের মনে হলো কোনও কোনও বাচ্চার কান্নার মধ্যেও আছে সৌন্দর্য।
বেশ কিছুক্ষণ বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে থাকার পর জিজ্ঞেস করল আনোয়ার, ‘তুমি তো আমাকে চেন না, আমার সাথে গিয়ে কী করবে?’
‘আমি আপনার সাথে যাব,’ যেন একটাই কথা জানে ছেলেটা।
‘আচ্ছা, ঠিক আছে। আজ রাতে আমার সাথে থেকো। কাল তোমার মা- বাবাকে খুঁজে বের করব।’
ছেলেটা চোখ মুছল।
আশপাশে তাকিয়ে কুকুরগুলোকে আর দেখতে পেল না আনোয়ার।
সাধনা – ১৫
পনেরো
বড় রাস্তায় এসে রিকশা নিল আনোয়ার। ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বলল, ‘তোমার বাবা কী করেন?’
কিছুই বলল না ছেলেটা। তাকে আইসক্রিম কিনে দিয়েছে আনোয়ার, মহা আনন্দে আইসক্রিম খাচ্ছে সে।
‘তোমার বাসা কোন্ এলাকায়?’ আবার প্রশ্ন করল আনোয়ার।
এবারও জবাব দিল না ছেলেটা। চোখে কোনও দুশ্চিন্তা বা উত্তেজনার ছাপ নেই।
বাসায় পৌছে গেল আনোয়ার। পথিমধ্যে নতুন জামা ও প্যান্ট কিনে দিয়েছে ছেলেটাকে। এখন তাকে কোনওভাবেই পথশিশু বলে মনে হচ্ছে না। বরং মনে হচ্ছে কোনও ধনী পরিবারের সন্তান।
‘তোমার নামটা বলবে?’ বলল আনোয়ার।
ছেলেটা স্পষ্ট গলায় বলল, ‘আমার নাম রাইয়ান।’
‘রাইয়ান শব্দের মানে জানো?’
‘বেহেশতের একটা দরজার নাম রাইয়ান।’
‘ও।’ বিস্মিত হয়েছে আনোয়ার। বস্তির ছেলের নাম এত আধুনিক হবে? কথাবার্তাও শুদ্ধ, স্বাভাবিক। কোথায় যেন একটা খটকা লাগছে।
রাইয়ানকে আরও কিছু প্রশ্ন করল আনোয়ার। কিন্তু জবাব দিল না ছেলেটা। পরিবারের অন্যরা তিনতলায় থাকলেও, ছাদের চিলেকোঠার রুমে থাকতে পছন্দ করে আনোয়ার। রাইয়ানকে বলা সত্ত্বেও সে তিনতলায় ঘুমাতে রাজি হলো না। সে চায় আনোয়ারের সাথে ঘুমাতে।
বিছানায় শরীর এলিয়ে দেয়ার কিছুক্ষণের ভেতর ঘুমিয়ে পড়ল রাইয়ান। কিন্তু চোখে ঘুম নেই আনোয়ারের। মনে অনেক প্রশ্ন। কাগজ-কলম নিয়ে লেখার তেমন অভ্যাস নেই ওর, তাই মনে-মনেই সাজাতে থাকল কিছু প্রশ্ন-উত্তর।
প্রথম প্রশ্নঃ ছেলেটার বয়স ছয় বা সাতের বেশি হবে না। কিন্তু তার কথাবার্তার ভঙ্গি প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মত। কেন?
উত্তর: হয়তো ছেলেটা নিয়মিত স্কুলে যায়। মা-বাবা গরিব হলেও কার্পণ্য করেনি ছেলেকে স্কুলে পাঠাতে।
কিন্তু এই উত্তর পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য মনে হলো না ওর।
দ্বিতীয় প্রশ্ন: একটা বাচ্চা ছেলে যে পথে-পথে বড় হয়েছে, সে তার বাসার ঠিকানা জানে না, এটা কীভাবে সম্ভব? যদি ধরেই নিই, সে আসলে বাসার ঠিকানা জানে না, তবে সে নিশ্চয়ই মা-বাবার নাম বলবে বা অন্তত এলাকার নাম বলবে। এসব বলছে না কেন?
উত্তর: ছেলেটা সবই জানে। কিন্তু বলতে ভয় পাচ্ছে।
তৃতীয় প্রশ্নঃ ছেলেটা ওর সাথে আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল কেন? রাস্তায় আরও অনেক মানুষ ছিল। কিন্তু ছেলেটা তার সাথেই কেন যেতে চাইল? আর কেনই বা সে পালিয়ে গেল না?
উত্তর: কোনও উত্তর জানা নেই।
চতুর্থ প্রশ্ন: কুকুর বিষয়ক রহস্যটা কি? ওগুলো একটা নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত যেতে বাধ্য করেছে ওকে। তারপর সেগুলোকে আর দেখা যায়নি।
উত্তর: ওগুলো সাধারণ কুকুরই ছিল। আনোয়ারকে কোথাও নিয়ে যায়নি। পুরো বিষয়টা হয়তো মনের ভুল।
পঞ্চম প্রশ্ন: আচ্ছা, এমন কি হতে পারে, কিডন্যাপ করা হয়েছে বাচ্চাটাকে? উত্তর: না। এটা সঠিক নয়। সেরকম হলে ছেলেটা তার মা-বাবার কাছে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল থাকত।
ষষ্ঠ প্রশ্নঃ ও যখন ছেলেটাকে ঘুমানো অবস্থায় দেখতে পায়, তখন তার শ্বাস- প্রশ্বাসের কোনও লক্ষণ ছিল না। এটা কীভাবে সম্ভব?
উত্তর: ছেলেটার দেহ সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছিল। তাই শ্বাস- প্রশ্বাসের বিষয়টি শতভাগ নিশ্চিত হয়ে বলা যায় না। আবার এমনও হতে পারে, ছেলেটাকে কোনও ঘুমের ওষুধ বা অন্য কিছু খাওয়ানো হয়েছিল। অনেক ওষুধ আছে, যার প্রভাবে ধীর হয়ে যায় মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি 1
সপ্তম প্রশ্ন: মহিলাটা বাচ্চা ফেলে পালাল কেন?
উত্তর: এর সহজ উত্তর হচ্ছে, সে প্রতারক। সত্যিকারের মা কখনও শত বিপদেও সন্তানকে ফেলে পালিয়ে যায় না।
প্রশ্নগুলো মাথায় নিয়েই রাইয়ানের দিকে তাকাল আনোয়ার। নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে বাচ্চাটা। ঘুমের ভিতরে হঠাৎ কিছু একটা বলে ফেলল।
কথাটা শুনে চমকে উঠল আনোয়ার।
রাইয়ান বিড়বিড় করে বলছে: ‘Revenge! I want revenge!’
এ কথার মানে কী?
সারারাত ঘুম হলো না আনোয়ারের, পায়চারি করতে লাগল ছাদে।
ষোলো
সকালে নাস্তা করে তিনতলায় বসে কার্টুন দেখতে লাগল রাইয়ান। এই মুহূর্তে চাকর-বাকর ছাড়া অন্য কেউ নেই আনোয়ারদের বাসায়। এই মুহূর্তে ব্যবসার কাজে সিঙ্গাপুরে আছে তার বাবা। আর অনেক আগেই মাকে হারিয়েছে সে।
রাইয়ানের দিকে তাকিয়ে বলল আনোয়ার, ‘চলো, তোমার মা-বাবাকে খুঁজতে বের হব।’
‘আমি যাব না।’
‘মানে? তুমি তোমার মা-বাবার কাছে যেতে চাও না?’
‘না।’
‘কেন?’
কিছু না বলে কঠোর চোখে দেখল রাইয়ান। এত ছোট বাচ্চা এভাবে তাকাতে পারে, চিন্তাতেও ছিল না আনোয়ারের। কেন জানি চোখ নামিয়ে নিতে বাধ্য হলো। রাইয়ান তার বাসায় থাকায় বিশেষ কোনও ক্ষতি হচ্ছে না। তবে তার মা-বাবাকে খুঁজে বের করতে হবে।
কেন ছেলেটা তার মা-বাবার কাছে যেতে চায় না?
তারা কি কোনও অত্যাচার করে?
কী জানি!
আগে খুঁজে বের করতে হবে রাইয়ানকে ফেলে পালিয়ে যাওয়া ওই মহিলাকে। কিন্তু দুই কোটি মানুষের মস্ত ঢাকা শহরে কোথায় খুঁজে পাবে তাকে?
অবশ্য চেহারা ভালভাবেই মনে আছে। ক্যাপটা মাথায় চাপিয়ে বেরিয়ে পড়ল আনোয়ার। বাড়ির বাবুর্চিকে বলে দিয়েছে, ঠিকমত দেখে রাখতে বাচ্চাটিকে।
রাইয়ানকে ফেলে যাওয়া ওই মহিলা বা মা-র সাথে নিজের কথোপকথন মনে করল আনোয়ার। মহিলা বলেছিল, তারা থাকে কাছের কোনও বস্তিতে। গত রাতে রাইয়ানকে পেয়েছে বনানীর সরু এক রাস্তায়। সেক্ষেত্রে খোঁজ নেয়া যেতে পারে বনানী বস্তিতে। কিন্তু তার আগে বনানীর সেই রাস্তায় আরও একবার যাওয়া দরকার। হয়তো ওই মহিলা সম্পর্কে জরুরি কোনও তথ্য দিতে পারবে ওখানকার মানুষ।
অনেক খোঁজ-খবর নেয়ার চেষ্টা করল আনোয়ার, কিন্তু নিশ্চিত করে কিছুই বলতে পারল না কেউ। অগত্যা সে ঠিক করল, ঢুঁ দেবে বনানী বস্তিতে। ওখানে খোঁজ নেয়ার কাজটাও সহজ হলো না। পদে-পদে বিভিন্ন আপত্তিকর কথা শুনতে হলো আনোয়ারকে। সবাই স্পষ্টভাবে বলল, রাইয়ানের মা নামে কেউ এখানে থাকে না। কেউ কেউ উচ্চারণই করতে পারল না রাইয়ানের নাম, বলল রায়হান। রাইয়ানের মা-র চেহারার বর্ণনাও দিল আনোয়ার, কিন্তু কাজ হলো না তাতেও। অনেকেই সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাতে লাগল তার দিকে! একজন তো বলেই বসল, ‘মেয়েছেলে দিয়া আপনার কাম কী?’
এসব কথায় দমল না আনোয়ার। খুঁজে বের করতেই হবে রাইয়ানের মা- বাবাকে।
ঢাকার আরও কয়েকটি বস্তিতে খোঁজ নিল আনোয়ার, কিন্তু ফলাফল শূন্য। ক্লান্ত হয়ে রাতে বাসায় ফিরল ও।
আনোয়ারকে দেখে দৌড়ে এল বাড়ির কেয়ারটেকার, বাবুর্চি ও কাজের মেয়ে।
‘কী হয়েছে?’ জিজ্ঞেস করল আনোয়ার।
মাথা নিচু করে বলল বাবুর্চি, ‘আপনি যে বাচ্চাটাকে রেখে গিয়েছিলেন, তাকে খুঁজে পাচ্ছি না!
‘কতক্ষণ ধরে খুঁজে পাচ্ছ না?’ উদ্বিগ্ন গলায় জিজ্ঞেস করল আনোয়ার। ‘ঘণ্টা দেড়েক হয়েছে।’
‘বাসার সব জায়গায় দেখেছ?’
‘হ্যাঁ।’
‘মেইনগেট বন্ধ ছিল?’
‘হ্যাঁ, ছিল।’
‘ছাদে যায়নি তো?’
‘ছাদ তো আপনি তালা দিয়ে গেছেন। যাওয়ার উপায় নেই।’
রাগে মুখে থুতু জমল আনোয়ারের। ইচ্ছা হলো সবগুলোর মুখে চড় বসিয়ে দিতে। অনেক কষ্টে দমন করতে হলো ইচ্ছেটাকে। উধাও হয়ে যেতে পারে না একটা বাচ্চা। আনোয়ার ভাবল, আগামীকাল সকাল পর্যন্ত আশপাশে খুঁজে দেখবে, তারপর জানাবে পুলিসে। এতে বাড়তি কিছু সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে, কিন্তু উপায় নেই।
বাইরে রাইয়ানকে খুঁজতে যাওয়ার আগে ছাদ ঘুরে দেখতে চাইল আনোয়ার। অবাক হয়ে লক্ষ করল, ছাদের দরজা খোলা, ওদিকে অন্ধকার। কেন জানি, মনে হলো অন্ধকারটা অন্য রাতের চেয়ে একটু বেশি গাঢ়! আস্তে-আস্তে এগিয়ে গেল আনোয়ার। কাঁপা গলায় বলল, ‘রাইয়ান।’
জবাব দিল না কেউ।
আবার বলল আনোয়ার, ‘রাইয়ান।’
অস্ফুট স্বরে কেউ বলল, ‘উঁ?’
‘রাইয়ান, তুমি কোথায়?’
‘তোমার ঘরে।’
আনোয়ার দেখল ছাদের চিলেকোঠার ঘরের দরজা খোলা, তালা নেই। অন্ধকার দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল ও, ‘তুমি এখানে কী করছ? ঢুকলে কীভাবে?’
জোরে হাসল রাইয়ান।
শরীরটা কেমন যেন শিরশির করে উঠল আনোয়ারের। রুমের বাতি জ্বালতে গিয়ে দেখল, নষ্ট হয়ে গেছে বাতি।
‘রাইয়ান, তুমি কোথায়? আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না।’
‘চোখ থাকতেও দেখতে পাচ্ছ না?’
‘না। খুব অন্ধকার।’
‘হা-হা-হা!’ হাসিটা যেন ছড়িয়ে পড়ল বহুদূরে।
‘হাসছ কেন?’
‘অন্ধকার ভয় লাগে তোমার?’
‘তুমি এসব কী বলছ?’
‘এবার বাতি জ্বালো। বাতি জ্বলবে।’
আবার সুইচ টিপল আনোয়ার। সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠল ঘরের বাতি। কিন্তু ঘরে নেই রাইয়ান!
তা হলে এতক্ষণ কার সাথে কথা বলল? দৌড়ে বেরিয়ে এসে আনোয়ার দেখল, ছাদের এক কোনায় দাঁড়িয়ে আছে রাইয়ান।
‘রাইয়ান,’ নরম সুরে ডাকল আনোয়ার।
পেছন ফিরে তাকাল রাইয়ান
‘তুমি…এ-এখানে কী করছ?’ জিজ্ঞেস করল আনোয়ার।
‘বাসায় ভাল লাগছিল না, তাই ছাদে এসেছি।’
‘কিন্তু ছাদে তো তালা দেয়া ছিল।’
‘আমি কোনও তালা দেখতে পাইনি।’
রাইয়ানের কথা শুনে সচকিত হলো আনোয়ার। বয়স্ক মানুষের মত কথা বলছে বাচ্চাটি। যেন কোনও শিশুর মধ্যে ঢুকে গেছে কোনও বয়স্ক মানুষ!
নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করে বলল আনোয়ার, ‘চলো, নিচে যাই।’
আপত্তি করল না রাইয়ান, হাঁটতে লাগল ধীর পায়ে।
আবারও বলল আনোয়ার, ‘তুমি নিচে যাও, আমি আসছি।’
নিচে চলে গেল রাইয়ান। নিজের রুমটা ভালভাবে দেখল আনোয়ার। নাহ্, কোনও অস্বাভাবিক কিছু নেই। এবার টর্চ হাতে ঘুরে দেখতে লাগল ছাদটা। হঠাৎ কয়েকটা ধাতব জিনিস দেখল ও। সেগুলো তুলে নিল হাতে। নিজের অজান্তেই বলল, ‘ওহ, মাই গড!’
এ কথা বলার কারণ, ওর সামনে খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে পড়ে ছিল তালার দুটো টুকরো!
সতেরো
ধীরে-ধীরে চোখ মেলে দেখল আনোয়ার। আজ তিনতলায় ঘুমিয়েছে সে। বাসার গেস্টরুমে ছিল রাইয়ান। কাল সারারাত নানা দুঃস্বপ্ন দেখেছে আনোয়ার। সবকিছু কেমন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। তালা খণ্ড-বিখণ্ড হওয়ার কারণও বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে, কেউ যেন প্রবল আক্রোশে ভেঙেছে তালা। রাইয়ানের মধ্যে কি কোনও রহস্য লুকিয়ে আছে? নাকি একটু বেশি-বেশি চিন্তা করছে আনোয়ার?
ঘড়িতে নয়টা ছুইছুই। রাইয়ান এখনও ঘুমাচ্ছে। উঠে পড়ল আনোয়ার আজ আবারও খুঁজতে বের হবে রাইয়ানের মা-বাবাকে। বাসার সবাইকে বলেছে, রাইয়ানের দিকে নজর রাখতে। আর আজকে কোনও তালা দেয়া হয়নি ছাদে। ফ্রেশ হয়ে রাইয়ানকে ঘুম থেকে ডেকে তুলল আনোয়ার। এক ডাকেই জেগে গেল রাইয়ান, যেন আনোয়ারের জন্যই অপেক্ষা করছিল।
খাওয়ার টেবিলে বলল আনোয়ার, ‘রাইয়ান?’
‘হ্যাঁ।’
‘ঠিকঠাক বলো তো, তুমি কে? তোমার মা-বাবা কোথায় থাকেন?’
‘আমি জানি না।’
‘তুমি না বললে আমি পুলিসের কাছে যাব। তারা এসে তোমাকে নিয়ে যাবে।’
কোনও ভাবান্তর হলো না রাইয়ানের মধ্যে। নীরস গলায় বলল, ‘আমি না চাইলে কেউ আমাকে নিয়ে যেতে পারবে না।’
‘মানে?’
‘এই বাসায় আমি কিছুদিন থাকব। আমাকে জ্বালাতন করবে না।’
‘তুমি আসলে কে?’
‘তুমি আসলে কে?’ একই ভঙ্গিতে পাল্টা প্রশ্ন করল রাইয়ান।
‘আমি? আমি আনোয়ার।’
‘তুমি আনোয়ার, আর আমি জানোয়ার। হা-হা!’
‘আমি তোমার সব খবরাখবর বের করব।’
‘খুবই ভাল। বের করো। আমিও সব জানতে চাই।’
খাওয়ার টেবিল থেকে উঠে পড়ল আনোয়ার। ঠিক করেছে, খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে রাইয়ানের বাবাকে রমনা পার্কে। সত্যিই যদি এই ছেলের নাম রাইয়ান হয়, তার বাবার নামও ‘র’ অক্ষর দিয়ে শুরু হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। যেমন রায়হান, রমজান, রহমত, রহমান। একটা পরিকল্পনা করেছে আনোয়ার। বিশ্ববিদ্যালয় পড়াকালীন সময়ে প্রচুর সার্ভের কাজ করেছে ও। এখন সেই সার্ভের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চাইছে। একটা যেন-তেন প্রশ্নাবলী তৈরি করে অনানুষ্ঠানিক সেক্টরের ওপর করা যেতে পারে ভুয়া সার্ভে। অনানুষ্ঠানিক সেক্টরের উত্তরদাতা হিসাবে নিতে হবে রমনা পার্কের চা-সিগারেট বিক্রেতাদেরকে। হয়তো এর মাধ্যমেই রাইয়ানের বাবাকে খুঁজে বের করা যাবে। প্রশ্নাবলীতে মূল বিষয় যেটি থাকবে, তা হলো নাম, ঠিকানা, ছেলে কয়জন, তাদের নাম, মোবাইল নাম্বার, আয়-ব্যয় ইত্যাদি। খুব সহজ সাধারণ তথ্য। প্রতিটি মানুষকে কিছু টাকাও দিতে হবে। কারণ এমনিতে সময় নষ্ট করে সঠিক তথ্য দিতে চাইবে না কেউ।
রমনা পার্কে গিয়ে প্রথমেই এক চা বিক্রেতার সাথে খাতির করে ফেলল আনোয়ার। তার কাছ থেকে দুই কাপ চা তো নিলই, এ ছাড়া বকশিস হিসাবে দিল পঞ্চাশ টাকা। চা বিক্রেতার নাম ইলিয়াস। সে এত টাকা বকশিস পেয়ে খুশিতে হয়ে গেল আত্মহারা। আনোয়ার বলল, ‘ইলিয়াস, রমনা পার্কে কতজন চা-সিগারেট বিক্রি করে?’
‘তা, স্যর, সাত-আটজন তো হবেই।’
‘সবার নাম জানো?’
‘হ্যাঁ, জানি।’
এদের সবাইকে কখন পেতে পারি?’
‘কেন, স্যার? কী দরকার?’
‘আমি একটা সার্ভে মানে জরিপ করব। এই সবার নাম, ঠিকানা, আয়-ব্যয় নিয়ে একটু তথ্য নেব আর কী। তুমি কি সবাইকে এক জায়গায় হাজির করতে পারবে?’
‘এইডা তো, স্যর, একটু কঠিন। তবে আশা করি, আপনি বারোটার দিকে সবাইকেই পাবেন। এই সময়ে কাস্টমার থাকে না, সবাই বসে-বসে ঝিমায়।’
‘আমি সবাইকে এক শ’ টাকা করে দেব। তুমি আজ বারোটায় সবাইকে এক জায়গায় হাজির করতে পারবে?’
‘হ্যাঁ, পারুম।’
‘ঠিক আছে, এখন বাজে সাড়ে দশটা। আমি পার্কে এই বেঞ্চেই বসে থাকব। তুমি সবাইকে এখানে নিয়ে আসবে।’
‘ঠিক আছে, স্যর।’
‘দেখি আরেক কাপ চা দাও।’
আনোয়ারের চোখে চশমা, হাতে কাগজ-পত্র ও কলম। কেউ যেন সন্দেহ না করে। যদি রাইয়ানের বাবা একবার তার আসল উদ্দেশ্য টের পায়, তবে নিশ্চিত পালিয়ে যাবে।
আঠারো
দুপুর বারোটায় অবাক না হয়ে পারল না আনোয়ার, আসলেই এলেম আছে ইলিয়াসের। সে সঠিক সময়েই আনোয়ারের সামনে হাজির করল সবাইকে। কেউ-কেউ অবশ্য প্রচণ্ড বিরক্ত, সার্ভের বিষয়টি তারা ভালভাবে বোঝেনি। কিন্তু কিছু কথা বললেই এক শ’ টাকা পাবে ভেবে এসেছে।
সবার দিকে তাকিয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে বলল আনোয়ার, ‘সবাই এসেছে? কেউ কি বাকি আছে?’
ইলিয়াস বলল, ‘না, স্যর। কেউ বাকি নাই।’
সবাইকে বিষয়টা সহজ ভাষায় বুঝিয়ে দিল আনোয়ার। সে কিছু প্রশ্ন করবে, তার ঠিকঠাক জবাব দিতে হবে। এরপর সবাই চলে যেতে পারবে পকেটে এক শ’ টাকা পুরে।
সবাই প্রশ্ন শুনে খুব আগ্রহী হয়ে উঠল। সহজ স্বাভাবিক প্রশ্ন। নাম, ঠিকানা, ছেলে-মেয়ে, এ বিষয়ে প্রশ্ন। মোট সাতজনের সাথে কথা বলতে আনোয়ারের লাগল পঞ্চাশ মিনিট। দেখল সাতজনের চারজনই কিশোর। এখনও বিয়ে করেনি। তাই চারজনকে মনে-মনে বাতিল করে দিল আনোয়ার। বাকি তিনজন বিবাহিত। তারা হচ্ছে ইলিয়াস, কাদের এবং রইস। এই তিনজনের একজন রাইয়ানের বাবা হতে পারে। কিন্তু আনোয়ার হতাশ হয়ে লক্ষ করল, এদের কারও সন্তানের নামই রাইয়ান নয়। আবার এমনও হতে পারে, মিথ্যা বলেছে রাইয়ান। তার আসল নাম হয়তো রাইয়ান নয়। ইলিয়াস, কাদের এবং রইসকে বসিয়ে বাকিদের বিদায় করে দিল আনোয়ার। টাকা পেয়ে মহা খুশি ইলিয়াস। এই ব্যাপারে খুব উৎসাহী সে।
‘আপনাদের স্ত্রীদের সাথেও অল্প একটু কথা বলতে হবে, সে জন্যও অবশ্য টাকা দেব,’ বলল আনোয়ার।
রইস বিরক্ত হয়ে বলল, ‘মেয়েছেলের সাথে আবার কথা কী?’
‘তেমন কিছু না। তাদের কাজ, আয়-ব্যয় সম্পর্কে একটু তথ্য নেব।’
‘আমাদের কাছ থেকেই নেন।’
‘নাহ্। যার তথ্য তার কাছ থেকেই নিতে হবে।’
ইলিয়াস উৎসাহের সাথে বলল, ‘ঠিক আছে, স্যর, আজকেই চলেন।’
তিনজনের বাসাই পার্কের কাছাকাছি, জানতে পারল আনোয়ার। বলল, ‘চলো, আজকেই কাজটা সেরে ফেলি। এ জন্য আপনাদের আরও দু’ শ’ টাকা দেব।’
টাকার কথা শুনে চকচক করতে থাকে তিনজনেরই চোখ। কোনও কাজ না করেই একদিনে তিন শ’ টাকা উপার্জন বিশাল ব্যাপার। এবার উৎসাহ দেখাল সবাই।
প্রথমে সবাইকে নিয়ে ইলিয়াসের বাসায় গেল আনোয়ার। বাসায়ই ছিল ইলিয়াসের বউ। এক কিশোরী মেয়েকে বেরিয়ে আসতে দেখল আনোয়ার। এ রাইয়ানের মা নয়। সেখানে বেশি সময় ব্যয় করল না ও।
এরপর কাদেরের বাড়িতে গেল আনোয়ার। কাদেরের বউকে দেখেও আশাভঙ্গ হলো। সে দুই-এক কথা জিজ্ঞেস করে সরে পড়ল। কাদেরের বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটু উত্তেজনা অনুভব করছে আনোয়ার। এখন বাকি আছে একমাত্র রইস। তবে কি রইসই রাইয়ানের বাবা? ছেলে হারানোর কোনও শোক অবশ্য তার চোখে-মুখে নেই। কাদের ও ইলিয়াসকে টাকা বুঝিয়ে বিদায় করে দিল আনোয়ার।
রইসের বাসা বেশ খানিকটা দূরে। দশ-পনেরো মিনিট হাঁটতে হবে।
‘স্যর, আসলে আমার বাসা নাই, ফুটপাতেই সংসার, বলল রইস। ‘তাই নাকি!’
‘হ্যাঁ। আগে বাসা ছিল বনানীর বস্তিতে। কিন্তু একটা সমস্যায় পড়ে বদলাতে হলো বাসা। এত জলদি নতুন কোথাও বাসা পাই না। তাই কয়েক দিন ধরে ফুটপাতেই আছি।’
‘খুব কষ্ট হচ্ছে তা হলে।’
‘আর কষ্ট। এই কষ্টতেই জীবনডা শেষ হয়ে যাবে।’
রইস রাস্তার পাশে বেশ ভাল সংসার পেতেছে। সেখানে খেলাধুলা করছে ছোট দুটো ছেলে-মেয়ে।
রইস একটা পিঁড়ে বের করে আনোয়ারকে বসতে দিয়ে বলল, ‘ওদের মা পানি আনতে গেছে। একটু বসেন।’
আনোয়ার বসল। মিনিট পাঁচেক পর রইসের স্ত্রী সুফিয়া পানি নিয়ে এল। সে আনোয়ারকে তখনও ভালভাবে খেয়াল করেনি। হঠাৎ তার দিকে তাকাল আনোয়ার। হ্যাঁ, সেইদিনের সেই মহিলা, রাইয়ানের মা!
আনোয়ারকে চিনতে পেরে যেন আকাশ থেকে পড়ল রাইয়ানের মা। অতি দ্রুত রইসকে কানে-কানে কী যেন বলল। শুনে রইসের চোয়াল ঝুলে পড়ল। আমতা-আমতা করতে লাগল সে। দু’জনে এসে জড়িয়ে ধরল আনোয়ারের পা বলল, ‘স্যর, আমাদের মাফ করে দেন!’
‘তোমাদের তো পুলিসে দেব ঠিক করেছি।’
‘না-না, স্যর। এই কথা কইবেন না। আপনার ভয়ে বাসা বদলাইছি। মেরাজের বাপ আপনারে চিনলে বাড়িতে আনত না,’ বলল মহিলা।
‘ঠিক আছে, পুলিসে দেব না। তবে একটা শর্ত আছে।
‘কী শর্ত?’
‘আমাকে সব কথা সত্যি বলতে হবে। কিছুই গোপন করবে না।’
দু’জনের ভয় ও কান্না একটু কমল।
আবারও আনোয়ার বলল, ‘কী? বলবে তো? নইলে…’
‘না-না, স্যর, বলব। কিন্তু আমাদের পুলিসে দিয়েন না। জীবনে একটা অন্যায় করেই ধরা খাইছি,’ কাতর গলায় বলল রইস।
আনোয়ারের সরাসরি প্রশ্ন: ‘রাইয়ান কি তোমাদের ছেলে?’
‘রাইয়ান কে?’ পাল্টা প্রশ্ন করল রইস।
‘তোমরা যে ছেলেকে মৃত সাজিয়ে ভিক্ষা করছিলে, তার কথা বলছি।’
‘ওই পোলার নাম তো আমি জানি না। আর…’
‘আর?’
‘ওই পোলাকে আমরা লাশ সাজাইনি। ও মারা গেসিল।’
‘মানে?!’ উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে পড়ল আনোয়ার।
‘স্যর, আপনারে সব বলতাছি। কিন্তু আপনি আমাদের পুলিসে দিয়েন না।’
‘আচ্ছা, কথা দিলাম, পুলিসে দেব না। তোমাদের কোনও ক্ষতিও করব না।’
উনিশ
রইস পুরো ঘটনাটা বলল আনোয়ারকে। তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য হচ্ছে: রইস রমনা পার্কে কাজ করার সময় এক ধুরন্ধর লোকের সাথে তার পরিচয় হয়। নাম তার লোকমান। সে রইসকে বুদ্ধি দেয় কবর থেকে লাশ চুরি করার। প্রথমে বিষয়টা রইসের একদম পছন্দ হয়নি। কিন্তু লোকমান নানাভাবে বোঝাতে থাকল। একটা টাটকা লাশ চুরি করে আনলে বিশাল লাভ। অনেক দামে লাশটা বিক্রি করা যাবে। লোভের কাছে পরাজিত হয়েছিল রইস। কিন্তু কথা তুলল, ‘লাশটা কার কাছে বিক্রি করব?’
‘আমার কাছে আনলে, আমিই কিনে নেব,’ বলল লোকমান।
‘কত দেবেন?’
‘পাঁচ হাজার টাকা।’
রইস চিন্তা করে দেখল পাঁচ হাজার তার জন্য অনেক টাকা। একবার লাশটা চুরি করতে পারলেই …
এরপর কবরস্থানে কড়া নজর রাখছিল রইস। প্রায় প্রতিদিনই গড়ে ছয়- সাতজনের দাফন হয় কবরস্থানে। সে উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু কাঙ্ক্ষিত সুযোগ ধরা দিচ্ছিল না। সেদিন ছিল মঙ্গলবার। রইস দেখল কয়েকজন মানুষ এসেছে লাশ দাফন করতে। সে সুযোগ পেয়ে মিশে গেল লোকগুলোর সাথে। এক ছোট বাচ্চাকে দাফন করতে এসেছে সবাই। ভাল করে কবরটা দেখে রাখল রইস। এই কবরস্থানের আশপাশে তেমন কোন জনবসতি নেই। তার উপর আজ বৃষ্টি। কেউ এদিকে আসবে বলে মনে হয় না। সন্ধ্যার দিকে লাশটা চুরি করার মতলব তার।
পরিকল্পনা অনুযায়ী চুপিচুপি সন্ধ্যায় কবরস্থানে ঢুকল রইস এবং তার স্ত্রী। গতকাল রাতে কবরস্থানের ঝোপঝাড়ের মধ্যে কোদাল আর শাবল রেখে গিয়েছিল তারা। সারাদিনের বৃষ্টি আরও সহজ করে দিয়েছিল তাদের কাজকে। কোথাও দেখা যাচ্ছিল না কবরস্থানের পাহারাদারকে। এই লোকটা সন্ধ্যার দিকে নেশা করার জন্য বেরিয়ে পড়ে। তাই তাকে নিয়ে চিন্তা নেই। কাজে নেমে পড়ে রইস। তুমুল বৃষ্টি হচ্ছিল, তাই কারও আসারও সম্ভাবনা নেই। এই লাশটা তাকে চুরি করতেই হবে। তারা সঙ্গে করে এনেছে বড় একটা বস্তা। ওটার মধ্যেই লাশটাকে ভরে ফেলল। বস্তা কাঁধে চাপিয়ে ধীরে-ধীরে হাঁটতে থাকল রইস। কবরস্থানের পশ্চিম কোণে মস্ত বড় জারুল গাছ। সেই গাছের নিচে লোকমানের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল তারা। লোকটা আগেই বলে রেখেছিল, সন্ধ্যা সাতটার দিকে এসে নিয়ে যাবে লাশটা।
একঘণ্টা পার হয়ে গেছে, বৃষ্টিও থেমেছে বেশ আগে, কিন্তু দেখা নেই লোকমানের! এত কষ্টের পর ফল না মেলায় কেমন জেদ চেপে গিয়েছিল রইসের। এই লাশ নিয়ে এখন সে কী করবে? তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিল, লোকমানের বাসায় যাবে সে, আর রাস্তার পাশে লাশ নিয়ে বসে থাকবে সুফিয়া। এর মাধ্যমে লাশ দাফনের কথা বলে মানুষের কাছ থেকেও পাওয়া যাবে কিছু টাকা। আর এর মধ্যে লোকমানকে খুঁজে বের করবে রইস। ছোট বাচ্চাটার লাশ থেকে কাফনের কাপড় খুলে ফেলে সুফিয়া। নিজের ছেলের ছেঁড়া প্যান্টটা পরিয়ে দেয়। তারপর একসময় বনানীর ওই রাস্তায় আনোয়ারের সাথে দেখা হয়েছিল সুফিয়ার।
সাধনা – ২০
বিশ
কবরস্থানের গার্ডের কাছ থেকে রাইয়ান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানতে পারল আনোয়ার। লাশ চুরি হয়েছে তা ইতিমধ্যে রাইয়ানের পরিবারকে জানিয়েছে গার্ড, কিন্তু তারা এ বিষয়ে কোনও ভ্রুক্ষেপ করেনি।
এই মুহূর্তে রাইয়ানের বাবা মুবিন চৌধুরীর সামনে বসে আছে আনোয়ার। বেশ ক’দিন দেখা করতে চেয়েছে, কিন্তু সুযোগ মেলেনি। শেষপর্যন্ত আজ রাজি হয়েছেন মুবিন চৌধুরী, যদিও আনোয়ারের আসল উদ্দেশ্য নিয়ে বেশ সংশয়ে আছেন তিনি
মুবিন চৌধুরী আনোয়ারের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত মুখে বললেন, ‘আমার কাছে কী দরকার?’
শান্ত গলায় বলল আনোয়ার, ‘আসলে আপনার ছেলে রাইয়ান সম্পর্কে একটু আলাপ করতে এসেছি।’
মুবিন চৌধুরী বললেন, ‘রাইয়ান! রাইয়ানকে নিয়ে কী কথা?’
‘রাইয়ান কবে মারা গিয়েছিল, কীভাবে মারা গিয়েছিল, এই বিষয়টা আমি জানতে চাই।’
‘আমি এ বিষয়ে কোনও কথা বলতে চাই না।’ চোখ আরেক দিকে সরিয়ে নিয়ে বললেন মুবিন চৌধুরী। ‘আপনি আসলে কে, বলুন তো?’
‘রাইয়ানের লাশ চুরি হয়েছে, জানেন তো?’
ভয়ের ছায়া পড়ল মুবিন চৌধুরীর চেহারায়। তিনি ভীত গলায় বললেন, ‘আপনি কি গোয়েন্দা বিভাগের কেউ?’
মাথা নেড়ে বলল আনোয়ার, ‘আমি গোয়েন্দা নই।’ একটু বিরতি দিয়ে বলল, ‘আসলে রহস্যময় এবং ব্যাখ্যাতীত বিষয়গুলো সম্পর্কে এক ধরনের আগ্রহ আছে আমার। নিতান্ত কৌতূহল থেকেই এসব বিষয়ের পিছনে ঘুরে বেড়াই।’
‘এর সাথে রাইয়ানের কী সম্পর্ক?’
‘আমার মনে হচ্ছে, রাইয়ানের মধ্যে এক ধরনের রহস্য ছিল, যেটা আপনি জানেন।’
‘এমন কিছু আমার জানা নেই। আর নিজের পারিবারিক বিষয়ে আপনার সাথে কথা বলব না।’ কড়া গলায় বললেন মুবিন চৌধুরী, ‘আপনি এখন আসুন।’
অনেকভাবে বোঝাতে চেষ্টা করল আনোয়ার, কিন্তু মুবিন চৌধুরী অনড়। পারিবারিক বিষয়ে তিনি কোনও কথা বলবেন না।
শেষ চেষ্টা করল আনোয়ার। ‘আপনি কি জানেন, আপনার ছেলে রাইয়ান বেঁচে আছে?’
ভয়ানকভাবে চমকে উঠলেন মুবিন চৌধুরী। মুহূর্তেই ফ্যাকাসে বর্ণ ধারণ করল মুখমণ্ডল। এক দৃষ্টিতে আনোয়ারের দিকে চেয়ে রইলেন। বললেন, ‘কী বললেন? রাইয়ান বেঁচে আছে?!’
‘হ্যাঁ, সবই বলব,’ জবাবে বলল আনোয়ার। ‘তবে তার আগে আমার কৌতূহল মেটাবেন আপনি। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর চাই।’
মুবিন চৌধুরীকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তাঁকে গ্রাস করেছে এক রাশ অস্বস্তি। চোখেমুখে বিষণ্ণতার ছায়াও পড়ল। নিচু গলায় ডাকলেন স্ত্রী মরিয়মকে। এমন ভাবে, যেন স্ত্রী না এলেই খুশি হতেন। সবকিছু ছাপিয়ে ক্লান্তির ছাপই ফুটে উঠেছে মরিয়ম বেগমের চেহারায়। অসম্ভব রূপবতী মহিলার চোখের নিচে কালি, চুলগুলো খানিকটা এলোমেলো। কিছু দিন আগে ছেলে হারিয়েছেন, চেহারায় এমন দুঃখ এবং ক্লান্তির ছাপ পড়াই স্বাভাবিক। মরিয়ম বেগম আনোয়ারের সামনে এসে বসলেন, ঠিক মুখোমুখি। মুবিন চৌধুরী মরিয়মের দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘যা সন্দেহ করেছিলাম, ঠিক তা-ই। উনি রাইয়ানের খোঁজ নিয়ে এসেছেন।’
মরিয়ম বেগমের চেহারা এক মুহূর্তে যেন বদলে গেল। ঘোরলাগা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আনোয়ারের দিকে। বললেন, ‘মৃত মানুষের কোনও খোঁজ থাকে না।
‘আপনাদের ছেলে রাইয়ান বেঁচে আছে,’ বলল আনোয়ার।
হিংস্র গলায় বললেন মরিয়ম বেগম, ‘মৃত রাইয়ান আমাদের ছেলে, জীবিত রাইয়ান নয়।’
কথাটার অর্থ ঠিক বুঝতে পারল না আনোয়ার। মুবিন চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করল সবকিছু খুলে বলতে।
বলতে শুরু করলেন মুবিন চৌধুরী, ‘আসলে রাইয়ান আমাদের নিজেদের সন্তান নয়। তিন মাস বয়সে আমরা ওকে এক এতিমখানা থেকে দত্তক এনেছিলাম। আমাদের আগের দুটি সন্তান ছিল। তবু আরও একটা সন্তানকে বুকে টেনে নেয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকেই রাইয়ানকে দত্তক নিই। রাইয়ানের সাথে অন্য বাচ্চাদের অনেক পার্থক্য ছিল। সে কখনও কাঁদত না। খিদে পেলেও না, ব্যথা পেলেও না। অন্ধকারে থাকতে পছন্দ করত। মাত্র এক বছর বয়সে দৌড়াতে পারত, আর দুই বছর বয়সে কথা বলতে শুরু করল। ছোট বাচ্চাদের মত আধো- আধো কথা না। কঠিন-কঠিন বাক্য বলত, আচার ও ভঙ্গিও ছিল বড়দের মত। প্রথম চার বছর কোনও সমস্যা ছাড়াই পার করেছিলাম আমরা। তবে ওর মধ্যে ছিল কিছু অস্বাভাবিকতা। ওর বয়স যখন তিন বছর, তখন বড় অস্বাভাবিক ঘটনাটি লক্ষ করলাম।’
‘কী ঘটনা?’ জিজ্ঞেস করল আনোয়ার।
‘তিন বছর বয়সে আমরা লক্ষ করলাম, রক্ত জিনিসটার প্রতি রাইয়ানের আগ্রহটা চোখে পড়ার মত। নিজের শরীরের কোথাও কেটে গেলে, সে খুঁচিয়ে- খুঁচিয়ে বড় করে ফেলত ক্ষতটাকে। তার নাকি ভাল লাগে রক্ত দেখতে। যেসব সিনেমায় ভায়োলেন্স বা রক্তারক্তি বেশি, সেগুলো আগ্রহ নিয়ে দেখত সে। আমরা ভাবতাম, ছোট মানুষ, হয়তো এসব দৃশ্য দেখে ভয় পাবে, কিন্তু ঘটত তার উল্টো। আমাদের বাড়িতে প্রায়ই মুরগি কিনে এনে জবাই করা হতো। আমি নিজ হাতেই মুরগি জবাই করতাম। রাইয়ান খুব আগ্রহ ভরে দৃশ্যটা দেখত এবং অনেক সময় নিজেই ছুরি হাতে জবাই করতে চাইত মুরগি। চেঁচিয়ে বলত, ‘আমাকে দাও! আমাকে দাও!’ এরপর রাইয়ানের বয়স যখন চার, তখন থেকেই মূলত সূত্রপাত হলো ভয়ঙ্কর সব ঘটনার।’ কথা থামিয়ে মুবিন চৌধুরী ঢক ঢক করে খেয়ে নিলেন এক গ্লাস পানি। বোঝা যাচ্ছে, বিষয়গুলো বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন না তিনি।
আবারও বলতে শুরু করলেন মুবিন চৌধুরী: ‘চার বছর বয়সে রাইয়ান ধারাল এক ছুরি নিয়ে আমাদের বাসার বেড়ালটার মাথা কেটে ফেলেছিল। শুধু মাথা কেটেই ক্ষান্ত হয়নি, সে বিড়ালের পুরো দেহটাও খণ্ড-বিখণ্ড করেছিল। ছোট বাচ্চারা যেমন কোনও কাজ করে সবাইকে আগ্রহ নিয়ে দেখাতে থাকে, তেমনি রাইয়ানও সেদিন আগ্রহ করে সবাইকে দেখাতে থাকে বিড়ালের খণ্ড-বিখণ্ড দেহ। তার পুরো শরীর রক্তে ভেজা। এই দৃশ্য দেখার জন্য আমি এবং আমার স্ত্রী, কেউই প্রস্তুত ছিলাম না। রাইয়ানের আচরণে হতবাক আমার অন্য দুই ছেলে-মেয়েও। চার বছর হওয়ার পর থেকেই প্রতিটা দিন যেন বদলে যেতে লাগল, রাইয়ান। বাসার অন্ধকার কোণগুলোতে লুকিয়ে থাকত। আর রক্ত সম্পর্কিত অস্বাভাবিকতা বাড়ছিল দিন-দিন। মাঝে-মাঝে আনমনে বিড়বিড় করে নিজের সাথে কথা বলত। এর মধ্যে আমার স্ত্রী একটা স্বপ্ন দেখল। ভয়ঙ্কর দর্শন এক প্রাণী মানুষের গলায় বলছে, ‘আমার ছেলেকে তোরা কেড়ে নিতে চেয়েছিলি, কিন্তু পারবি না।’ স্বপ্ন নিয়ে বিচলিত হওয়া ঠিক নয়, কিন্তু সার্বিক পরিস্থিতিতে আমরা চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। রাইয়ানের মধ্য থেকে পুরোপুরি হারিয়ে গেল স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটা। সে হাসতে ভুলে গেল, খেলাধুলো করত না, ঠিকমত কথা বলতেও চাইত না। খাওয়া-দাওয়াও তেমন করত না। এই অবস্থায় আমরা ভাবলাম, কোনও মানসিক ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব ওকে। কিন্তু রাইয়ান কীভাবে যেন টের পেয়ে গেল বিষয়টা, কোনওভাবেই রাজি হলো না ডাক্তারের কাছে যেতে। এভাবেই পার হলো খারাপ একটা বছর। এরপর রাইয়ানের বয়স যখন পাঁচ হলো, তখন…’ চুপ হয়ে গেলেন মুবিন চৌধুরী।
আনোয়ার বলল, ‘তখন কী?’
‘তখন হুট করেই মারা গেল সে।’
বিস্মিত হয়ে বলল আনোয়ার, ‘মারা গেল?!’
কপালের ঘাম মুছে মুবিন চৌধুরী বললেন, ‘হ্যাঁ, মারা গেল। আজ থেকে ঠিক এক বছর আগের কথা বলছি। একদিন সকালে রাইয়ান ঘুম থেকে উঠতে দেরি করলে কেমন যেন সন্দেহ হয় আমাদের। অনেক ডেকেও কোনও সাড়াশব্দ পাচ্ছিলাম না। পরবর্তী সময়ে দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকি আমরা। দেখলাম বিছানায় এলিয়ে পড়ে আছে রাইয়ানের শরীরটা। ঠাণ্ডা হয়ে আছে সারাশরীর। প্রাণের কোনও চিহ্ন নেই চেহারায়। দ্রুত গিয়ে একজন ডাক্তার নিয়ে এলাম। ডাক্তার পাল্স, বিপি, চোখ দেখে বলল, ‘আপনাদের সন্তান আর বেঁচে নেই।’
‘এমন মৃত্যু আমাদের কারও কাম্য ছিল না। ভয়ঙ্করভাবে ভেঙে পড়লাম। কষ্টে যেন ফেটে যাচ্ছিল বুকটা। কী কোমল একটা মুখ, আর কোনও দিন ডাকবে না বাবা বলে। যত অস্বাভাবিকতাই থাকুক, সে তো আমাদের সন্তান। ডাক্তার চলে যাবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দাফনের প্রস্তুতি শুরু করলাম আমরা। রাইয়ানকে গোসল করানো হলো, কাফনের কাপড় পরানো হলো। আমরা যখন কবরস্থানের দিকে রওয়ানা দেব, তখন হঠাৎ উঠে বসল রাইয়ান। পুরো বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ল ভয়ের পরিবেশ। কেউ-কেউ সহজভাবে মেনে নিতে পারছিল না ওকে। মুহূর্তেই খালি হয়ে গেল পুরো বাড়ি। আমার দুঃখের অনুভূতিও কেমন যেন রূপান্তরিত হলো ভয়ে। ডাক্তার যাকে মৃত ঘোষণা করল, সে কীভাবে বেঁচে উঠল? এ ঘটনার পর আমরা আর ভালভাবে গ্রহণ করতে পারিনি রাইয়ানকে।
‘রাইয়ান বেঁচে ওঠার পর ওর মধ্যে আসতে শুরু করল নানা পরিবর্তন 1 রেগে উঠত অল্পতেই। কারণে অকারণে আমার অন্য দুই ছেলে-মেয়েকে আঘাত করত। বিশ্ববিদ্যালয়ে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে আমার বড় ছেলেটা, আর মেয়েটা কলেজে, ফার্স্ট ইয়ারে। বয়সে বড় হওয়া সত্ত্বেও রাইয়ানের শক্তির কাছে হার মানতে হতো ওদের। প্রায়ই ঘরের অন্ধকার কোণে পদ্মাসনে বসতে দেখতাম রাইয়ানকে। মনে হতো যেন ধ্যান করছে। শত ডাকাডাকিতেও সাড়া দিত না। এভাবে পার হতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা।
‘আমাদেরও নানাভাবে কষ্ট দিতে থাকল রাইয়ান। তার কোনও কথাতে আপত্তি করলেই ভয়ঙ্করভাবে রেগে যেত। এমন কী আঘাত করতেও ছাড়ত না। ওর শক্তির কাছে অসহায় হয়ে পড়েছিলাম আমরা। আর ওর ইচ্ছার কাছে ছিলাম বন্দি। ওর সন্তুষ্টির জন্য প্রায়ই বাজার থেকে কিনে আনতে হতো জ্যান্ত মুরগি। ওগুলো সে নিজ হাতে জবাই করত। রক্ত মেখে নিত নিজের গায়ে। এসব কুৎসিত দৃশ্য আমাদের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব হচ্ছিল না। কিন্তু কী রকম এক অদ্ভুত পরিবর্তন লক্ষ করেছিলাম আমাদেরও মধ্যেও। রাইয়ান না চাইলে ঘর থেকেও বের হতে পারতাম না আমরা। অদৃশ্য কিছু যেন আঘাত করত আমাদেরকে। আস্তে-আস্তে আমরা বুঝতে পারলাম, অশুভ কোনও বিষয় আছে রাইয়ানের মধ্যে। কিন্তু এই অশুভ বিষয়টা কী আমরা নিশ্চিত ছিলাম না। মনে হচ্ছিল রাইয়ানকে দূরে সরিয়ে দেয়াই মঙ্গলজনক।
‘কিছুদিন আগে দ্বিতীয়বারের মত মারা গেল রাইয়ান। ওকে পরীক্ষা করে দেখল ডাক্তার, পুরো শরীর ঠাণ্ডা, হৃৎস্পন্দন নেই, পাও পাওয়া যাচ্ছে না। এবার আগের মত দেরি করিনি। বেশি লোক জানাজানিও হয়নি। মৃত্যুর তিন ঘণ্টার মধ্যেই দাফন করা হলো রাইয়ানকে। ওকে কবরে শুইয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু কবর দেয়ার পরদিন আমরা খবর পেলাম, চুরি হয়ে গেছে রাইয়ানের লাশ। আর আজকে আপনার কাছে শুনলাম, বেঁচে আছে ও।’
‘হ্যাঁ। রাইয়ান বেঁচে আছে। আমার কাছেই আছে।’
হাতজোড় করে বললেন মুবিন চৌধুরী, ‘আপনার কাছে অনুরোধ, আমাদের কাছে আনবেন না রাইয়ানকে।’
মন দিয়ে সব শুনেছে আনোয়ার। রুমের পেইন্টিংগুলো দেখতে দেখতে বলল, ‘রাইয়ান সম্পর্কে অজানা বিষয় জানতেই এসেছিলাম। আগেই বলেছি, এসব বিষয়ে আমার আছে প্রবল আগ্রহ। আপনাদের এসব তথ্য অনেক কাজে লাগবে আমার। আপনারা কি বলবেন কোন্ এতিমখানা থেকে এনেছিলেন রাইয়ানকে?’
নাম মনে করার চেষ্টা করলেন মুবিন চৌধুরী। কয়েক সেকেণ্ড পর বললেন, ‘হ্যাঁ, মনে পড়েছে। শ্যামলীর ভেতর দিকে এক এতিমখানা আছে, উত্তরখান এতিমখানা। সেখান থেকে এনেছিলাম।’
বিড়বিড় করে বলল আনোয়ার, ‘আমিও ছয় বছর আগে বাচ্চাটাকে রেখে এসেছিলাম ওই এতিমখানায়।’
‘কী বললেন?’
‘না, কিছুই না।’ আবার বলল আনোয়ার, ‘আপনি কি রাইয়ানের ধ্যানের বিষয়টি আরেকটু বিস্তারিতভাবে বলবেন?’
‘হ্যাঁ। ওকে প্রায়ই দেখতাম ধ্যানের ভঙ্গিতে বসে থাকতে। মাঝে-মাঝে বিচিত্র ভাষায় কী সব বলত।’
‘ধ্যানের বিষয়টা কত বছর বয়সে প্রথম লক্ষ করেছিলেন?’
একটু ভেবে মুবিন চৌধুরী বললেন, ‘সম্ভবত চার বছর বয়সেই প্রথম এই ধ্যানের বিষয়টি লক্ষ করি।’
‘আরেকটা প্রশ্ন, একটা সত্যি জবাব চাই।’
‘হ্যাঁ, বলুন।’
‘আপনারা কি কখনও রাইয়ানের সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করেছিলেন বা মারধর করেছিলেন?’
‘সন্তানকে মা-বাবা যে ছোটখাট শাসন করে, সেসব করতাম। আর…’
‘আর কী?’
‘রাইয়ানের চতুর্থ জন্মদিনের সময় ঘটেছিল একটা ঘটনা। হাই ব্লাডপ্রেশারের রোগী আমার স্ত্রী, সেসময়ে শারীরিক অবস্থা ভাল ছিল না তার। তাই, সেবার আমরা রাইয়ানের জন্মদিনে কোনও অনুষ্ঠান করব না বলে ঠিক করেছিলাম। কিন্তু রাইয়ান মানতে চাইছিল না বিষয়টা। একদম প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মত আমাদেরকে চার্জ করতে লাগল। আমার ছেলে-মেয়েদের সাথে ওর সম্পর্ক একদম মধুর ছিল না। তখন সবাই মিলে অনেক কটু কথা বলে ফেলেছিলাম ওকে।’
‘সম্ভবত ওই সময়েই রাইয়ান জানতে পারে, দত্তক আনা হয়েছিল তাকে। ঠিক না?’
আনোয়ারের বিচক্ষণ অনুমানে অবাক না হয়ে পারলেন না মুবিন চৌধুরী। বললেন, ‘জী, ঠিক। রাগ করে সেদিন কথাটা বলে ফেলেছিল আমার মেয়ে সভ্য। ‘তুই আমাদের আপন ভাই না, এ জন্যই মায়ের কষ্টের কোনও মূল্য নেই তোর কাছে।’’ মুবিন চৌধুরী অপরাধীর গলায় বললেন, ‘তবে বিশ্বাস করুন, আমরা কখনও ওকে আলাদা করে দেখিনি। আমার অন্য দুটি ছেলে-মেয়ে হয়তো একটু অবহেলা করেছে, কিন্তু আমরা তাদের অন্যায়কে প্রশ্রয় দিইনি।’
‘আজ অনেকগুলো হিসাব মিলে গেল,’ দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বলল আনোয়ার।
‘আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি উঠি।’
মূর্তির মত বসে রইলেন মুবিন চৌধুরী এবং তাঁর স্ত্রী, একবারও দেখলেন না আনোয়ারের দিকে।
আনোয়ার লক্ষ করল, চোখে পানি মরিয়ম বেগমের। হয়তো এই ভয়ঙ্কর সন্তানটিকে এখনও খুব ভালবাসেন তিনি।
একুশ
ডা. রাশেদের চেম্বারে ঢুকল আনোয়ার। এই মানুষটার সাথে খুব সখ্য রয়েছে তার। ডাক্তার হিসাবে রাশেদ যেমন প্রথম শ্রেণীর, মানুষ হিসাবেও। ঢাবির ছাত্র হলেও রাশেদের সাথে ঢাকা মেডিকেলে প্রচুর আড্ডা দিয়েছে আনোয়ার। ওর চেয়ে রাশেদ বয়সে একটু বড় হলেও সম্পর্কটা একদম বন্ধুর মত।
আনোয়ারকে দেখে উৎফুল্ল গলায় বলল রাশেদ, ‘কী, আনোয়ার, সরাসরি আমার চেম্বারে? কোনও বিশেষ দরকার?’
হেসে বলল আনোয়ার, ‘রাশেদ ভাই, একটা বিষয়ে কথা বলার জন্য আপনার কাছে এসেছি। আপনি যেমন আন্তরিকভাবে সবকিছু বুঝিয়ে বলবেন, অন্য জায়গায় এটা সম্ভব নয়, তাই জ্বালাতে এলাম।’
‘আরে, জ্বালানো বলছ কেন?’ চশমা খুলতে খুলতে বলল ডা. রাশেদ, ‘খুব খুশি হয়েছি। অনেকদিন দেয়া হয় না আড্ডা। তবে তোমাকে আধঘণ্টা বসতে হবে। আরও দু’জন রোগী দেখা বাকি।’
‘কোনও সমস্যা নেই, রাশেদ ভাই। আমি বাইরে বসছি।’
‘ঠিক আছে।’
চল্লিশ মিনিট পর ডাক পড়ল আনোয়ারের।
অনেকক্ষণ রোমন্থন চলল পুরনো স্মৃতির। এরপর হালকা স্ন্যাকস খেল দু’জন। ডা. রাশেদ হাত-পা ছড়িয়ে চেয়ারে বসল। এরপর বলল, ‘এবার বলো কী জানতে চাও?’
‘রাশেদ ভাই, মৃত মানুষ কি কখনও জীবিত হতে পারে? এমন কোনও বিষয় কি মেডিকেল সায়েন্সে আছে?’
গম্ভীর হয়ে গেল ডা. রাশেদ। কিছুক্ষণ ভেবে বলল, ‘না। মৃত মানুষ কখনও জীবিত হতে পারে না।’
‘তা হলে যে প্রায়ই পত্রিকায় পড়ি মৃত্যুর এত ঘণ্টা পর বেঁচে উঠলেন রোগী, আবার সেদিন পড়লাম পোস্টমর্টেমের সময় রোগী নড়ে উঠল। এসব বিষয়ে কী বলবেন?’
‘তোমাকে পুরো ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি। এর একটা যৌক্তিক ব্যাখ্যা আছে। ‘কী ব্যাখ্যা?
‘এরা আসলে মারা যায়নি, মানে এদের মৃতদের কাতারে ফেলা যায় না। এ ধরনের ঘটনাকে বলে স্থগিত মৃত্যু বা আপাত মৃত্যু। অনেকে এটাকে বলে পুনর্জীবিত স্থগিত মৃত্যু। প্রথমেই আসি পত্রপত্রিকায় আমরা যেসব খবর পড়ি, সে বিষয়ে। আসলে ডাক্তাররা প্রাথমিকভাবে বিপি, পাস্ চেক করেই ধরে নেয় মারা গেছে রোগী। কিন্তু সত্যিকার অর্থে কিছু রোগী তখনও মারা যায়নি। হয়তো খুব স্তিমিত গতিতে কাজ করছে তার হার্ট। এক্ষেত্রে নিশ্চিত হওয়ার জন্য করতে হয় ইসিজি। ওটা করলেই নিশ্চিতভাবে বোঝা যাবে, রোগী মারা যায়নি; তবে এসব ক্ষেত্রে রোগীর বেঁচে ফিরে আসার সম্ভাবনা খুবই কম।’
‘কেউ ইচ্ছাকৃত এ কাজ করতে পারে?’ জিজ্ঞেস করল আনোয়ার।
‘মানে?’
‘মানে, কেউ ইচ্ছাকৃত মৃত্যুবরণ করে আবারও জীবিত হতে পারে?’
‘বিষয়টা হাস্যকর শোনালেও উত্তরটা হচ্ছে: হ্যাঁ, পারে। অনেক মুনি, ঋষি, সাধুরা সাধনার মাধ্যমে নিজ শারীরবৃত্তীয় কাজকে বন্ধ করে দিতে পারে সাময়িকভাবে। এতে আপাতদৃষ্টিতে তারা মৃত মানুষের মত হয়ে যায়, আবার নির্দিষ্ট সময় পর সচল হয়ে ওঠে তাদের শরীর। ডা. রাশেদ মুখে হাত বোলাতে- বোলাতে বলল, ‘অনেকটা সাপ বা ব্যাঙের শীতযাপনের সাথে তুলনা করা যায় এর। কিছু মানুষের ক্ষেত্রে এটি বিশেষ এক ধরনের ক্ষমতা।’
‘কীভাবে অর্জন করা যায় এই ক্ষমতা?’
‘ধ্যান ও বিভিন্ন যোগ সাধনার মাধ্যমে অর্জন করা যায়। তবে প্রকৃতি প্রদত্ত কিছু বিষয়েরও প্রয়োজন হয়। সবাই এ কাজ করতে পারলে তো পৃথিবী জুড়ে আলোড়ন পড়ে যেত। এত সহজ নয় বিষয়টা।’
‘আপনি খুব সহজ করে বুঝিয়ে বলেন, রাশেদ ভাই। অনেক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলাম।’
‘তুমি কি এখনও ভূত, প্রেত, রহস্য নিয়ে পড়ে আছ?’ কৌতুকের সুরে জিজ্ঞেস করল ডা. রাশেদ।
উত্তর না দিয়ে হাসল আনোয়ার। আবার বলল ডা. রাশেদ, ‘তুমিই অবশ্য ভাল আছ। সারাদেশে ঘুরে বেড়াও, অ্যাডভেঞ্চার করো। কতই না আনন্দ। আর আমাদের নিজেদের জন্য সময় বলতে কিছু নেই।’
‘এবার আপনাকে নিয়ে একটা অ্যাডভেঞ্চারে যাব।’
‘সত্যি?’
‘হ্যাঁ। আগে হাতে একটা কাজ আছে, ওটা শেষ করে নিই, তারপর বিস্তারিত বলব আপনাকে।’
উঠে দাঁড়াল আনোয়ার।
ডা. রাশেদ বলল, ‘এত তাড়া কীসের? ডিনার করে যাও।’
‘না, ভাইয়া, একটু কাজ আছে। পরে আবার আসব।’
বাইশ
ঘড়িতে রাত দশটা বেজে বিশ মিনিট। একরাশ ক্লান্তি নিয়ে বাসায় ফিরেছে আনোয়ার। ভাল লাগছে না শরীরটা। সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। রাইয়ানের দিকে দৃষ্টি গেল। এক মনে টিভি দেখছে ছেলেটা।
আনোয়ারকে দেখে রাইয়ান বলল, ‘কী, আমার ব্যাপারে সব খোঁজ পেলে?’
জবাব দিল না আনোয়ার।
‘তোমার হাত থেকে রক্ত পড়ছে কেন?’ টিভির দিকে তাকিয়েই বলল রাইয়ান।
অবাক হয়ে নিজের ডান হাতের দিকে তাকাল আনোয়ার। সেখান থেকে এক নাগাড়ে ঝরছে রক্ত। ক্রমেই বাড়ছে ব্যথা। ক্ষতটা দেখে মনে হচ্ছে, ওর হাতের কয়েক জায়গায় ধারাল ছুরি দিয়ে পৌঁচ দিয়েছে কেউ। অথচ এতক্ষণ ক্ষতটা লক্ষই করেনি আনোয়ার। হাসছে রাইয়ান। আনোয়ারের মনে হচ্ছে, সে পরিচিত এই হাসির সাথে। এমন বিশ্রীভাবে হাসতে পারে না কোনও বাচ্চা ছেলে। আচ্ছা, ওর হাতের ক্ষতের সাথে কোনও যোগসূত্র নেই তো রাইয়ানের? হাতে অ্যান্টিসেপটিক লাগিয়ে ছাদে চলে গেল আনোয়ার। আজ রাতে নিজের ঘরে ছাদের চিলেকোঠায় থাকার ইচ্ছা ওর। কী যেন মনে করে তালা মেরে রাখল ছাদের দরজাটা।
রাতে হঠাৎ ভেঙে গেল আনোয়ারের ঘুম। চারপাশে গাঢ় অন্ধকার। পিপাসা পেয়েছে খুব। পানি ও আলোর পিপাসা এলোমেলো করে দিচ্ছে মনোজগৎকে। বিছানায় উঠে বসল। তখনই শুনতে পেল একটা মেয়ের কান্নার শব্দ।
আনোয়ার বলল, ‘কে…কে?’
থেমে গেল মেয়েটার কান্না। একটু পর আবারও শুরু হলো ফুঁপিয়ে উঠে কান্না।
কাঁপা গলায় বলল আনোয়ার, ‘কে কাঁদে? কে?’
‘আমি,’ ফোঁপাতে ফোঁপাতে জবাব দিল কোনও নারী কণ্ঠ।
‘আমি কে?’
‘আমি খেয়া।’
‘খেয়া?’ চিনতে পারল আনোয়ার। দোতলার ভাড়াটিয়া সোবহান সাহেবের ছোট মেয়ে।
‘হ্যাঁ।’
‘তুমি এখানে কীভাবে এলে?’
‘আমি জানি না।’
‘তাড়াতাড়ি বাসায় যাও।’
‘আমি উঠে দাঁড়ানোর শক্তি পাচ্ছি না।’
‘খেয়া, কেউ দেখে ফেললে কী ভাববে, বলো তো!’
আবার কাঁদতে লাগল খেয়া।
‘আস্তে, খেয়া, আস্তে,’ বলল আনোয়ার। ‘শব্দ কোরো না।’
খেয়ার কান্নার শব্দ একটু কমে এল, তবে পুরোপুরি মিলিয়ে গেল না। উঠে বসে বাতি জ্বালল আনোয়ার। কই, কেউ তো নেই! চিলেকোঠার দরজা খুলে এল ছাদে। নাহ্, ছাদেও কেউ নেই। ছাদের দরজাও তালাবদ্ধ। এখনও কাঁপছে ওর বুকটা। এসব কী দেখছে ও? ক্লান্ত ভঙ্গিতে নিজের রুমে ঢুকল আনোয়ার। এরপর যে দৃশ্যটি দেখল, তাতে কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে গেল ওর হৃৎস্পন্দন। ওর ঘরের সিলিং ফ্যানের সাথে ঝুলছে খেয়া। আত্মহত্যা করেছে। বেরিয়ে আছে জিভ। চোখ খোলা, বীভৎস এক দৃশ্য। বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারল না আনোয়ার, পড়ে গেল মাথা ঘুরে। ঠিক তখনই জোরে হেসে উঠল কে যেন! হাসিটা চিনতে পারল আনোয়ার। হাসছে রাইয়ান্! রাইয়ান ওর সাথে মজা করছে বুঝতে পারল আনোয়ার। এটা এক ধরনের খেলা।
পিশাচের হাসি হেসে বলল রাইয়ান, ‘আমাকে তুই চিনতে পেরেছিস? আমাকে জন্মের সাথে-সাথে এতিমখানায় ফেলে এসেছিলি তুই। আমার বাবার সাথে অনেক হিসেব-নিকেশ আছে তোর। আর আমার প্রিয় নানাজান মেরে ফেলতে বলেছিল আমাকে।’ কথাগুলো শুনতে-শুনতে চোখ বন্ধ হয়ে এল আনোয়ারের।
তেইশ
পরদিন সকালে নিজেকে বিছানায় আবিষ্কার করল আনোয়ার। মোবাইল ফোনের স্ক্রিনে দেখল, নুযহাতের বাবা রফিক সাদি ফোন দিয়েছেন ওকে। তিনি কানাডা চলে যাওয়ার পরেও প্রায় প্রতি মাসেই ফোন করতেন। তবে গত কয়েক মাস ধরে কোনও যোগাযোগ নেই।
আনোয়ারকে উৎফুল্ল গলায় রফিক সাদি বললেন, ‘আমরা গত পরশুদিন এসেছি দেশে। আমার সাথে নুযহাতও এসেছে।’
ভিতরের উত্তেজনা বুঝতে দিল না আনোয়ার, স্বাভাবিক গলায় বলল, ‘খুবই ভাল।’
‘তোমার সাথে দেখা হয়েছিল ছয় বছর আগে। এরপর আর দেশে আসা হয়নি, দেখাও হয়নি। নুযহাতকে বিয়ে দিয়েছি। নুযহাত খুব সুখে আছে। বাপ- মেয়ে দশদিনের জন্য চলে এলাম দেশের টানে।’
‘খুব ভাল করেছেন।’
‘অবশ্যই বাসায় আসবে। আমরা খুব খুশি হব তুমি কয়েকটা দিন আমাদের সঙ্গে থাকলে। কারণ, তুমি আমাদের অনেক আপন একজন। তোমার ঋণের কথা কখনও ভোলা সম্ভব নয়।
ফোনে নুযহাতও কথা বলল, ‘আনোয়ার ভাই, আপনাকে কয়েকটা দিন আমাদের বাসায় থাকতেই হবে। কোনও না শুনব না।’
আনোয়ার রাজি না হয়ে পারল না। ঠিক করল রাইয়ানকেও নিয়ে যাবে ওই বাসায়। কেন যেন ওর মন বলছে, ওই বাসাতেই রাইয়ান বিষয়ে লুকিয়ে আছে কোনও সমাধান।
সেই পুরানো স্মৃতি মনে পড়ল আনোয়ারের। নুযহাতের কথা, রফিক সাদির কথা, ঝমঝম কুঠির কথা, জয়নালের কথা, পিশাচের কথা।
দুপুরের দিকে খেয়ার সাথে দেখা হলো ওর। বুঝল, গতকাল যা দেখেছে, সবই ভ্রান্তি, চোখের ভুল। রাইয়ান একবারও জিজ্ঞেস করল না কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সব জানে।
রাইয়ানকে নিয়ে রফিক সাদির বাসায় যখন পৌছাল আনোয়ার, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রফিক সাদি বুকে জড়িয়ে ধরলেন আনোয়ারকে। কিছুক্ষণ কুশলাদি বিনিময়ে পার হলো। রাইয়ানের দিকে তাকিয়ে সরু চোখে বললেন রফিক সাদি,
‘এই ছেলেটি কে?’
তাঁর কানের কাছে মুখ এনে বলল আনোয়ার, ‘আপনাকে সব বলব। এখন কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।’ কথা ঘুরিয়ে উঁচু গলায় বলল আনোয়ার, ‘আপনি বলেছেন, তাই আপনার বাসায় কয়েকদিন থাকতে এলাম। কোন্ রুমে থাকব আমরা?’
.
আনোয়ার এবং রাইয়ানকে দুটো আলাদা রুমে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন রফিক সাদি। তাঁকে আলাদা রুমে ডেকে নিয়ে বলল আনোয়ার, ‘এই ছেলেটি কে, আপনি জানেন?’
‘কে, বলো তো! ওর দিকে তাকিয়েই বুকের ভিতরটা কেমন যেন কেঁপে উঠেছে।’
‘উত্তরটা শুনতে আপনার ভাল লাগবে না।’
‘তবু বলো। আমি শুনতে চাই।’
রফিক সাদিকে বলল আনোয়ার, ‘এই ছেলেটি আপনার নাতি।’
‘আমার নাতি? কী বলছ এসব?!’
‘হ্যাঁ।’
‘আমার কোনও নাতি নেই,’ মাথা দোলাতে-দোলাতে বললেন রফিক সাদি। কাজ করছে না মাথা। এতদিন পর দেশে এসে এ কী শুনছেন?
আবারও বলল আনোয়ার, ‘আপনি অস্বীকার করলেও সত্য সত্যই। এই ছেলেটি নুযহাতের সন্তান।’
‘না-না! নুযহাতের কোনও সন্তান নেই!
‘আপনি জোর দিয়ে বললেই তো সত্য কখনও মিথ্যা হবে না। নুযহাতের সাথে ছেলেটার চেহারার মিল নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন?’
‘এ নুযহাতের নয়, পিশাচের সন্তান,’ প্রচণ্ড রাগে চিৎকার করে বললেন রফিক সাদি, ‘তোমাকে বলেছিলাম বাচ্চাটিকে মেরে ফেলতে! তুমি ওই পিশাচটাকে মেরে ফেলোনি কেন?’
আনোয়ার বলল, ‘আমি পারিনি মারতে। মানুষ হয়ে হত্যা করা যায় না অন্য মানুষকে।’
‘বাহ! ভালই করেছ! আমার দেশে আসাই ভুল হয়েছে। এই আবর্জনা বেঁচে আছে জানলে কখনও ফিরতাম না।’
‘একটা এতিমখানায় রেখে এসেছিলাম রাইয়ানকে। কয়েক মাস পর ওখান থেকে একটি পরিবার ওকে দত্তক নেয়।’
‘তা হলে এতদিন পর তুমি কীভাবে একে খুঁজে বের করলে? সেই পরিবারের পরিচয়েই তো এর বড় হওয়ার কথা।’
‘রাইয়ানকে ঘিরে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সমস্যার পিছনে ছুটতে গিয়েই জেনে ফেলেছি ওর আসল পরিচয়।’
‘কী সমস্যা?’
‘আপনাকে পরে সব বলব।’
‘এই বাচ্চা যেখানেই যাবে, সৃষ্টি করবে সমস্যা। তুমি একবার আমাদের বাঁচিয়েছ। কিন্তু এবার তোমার ভুলেই আমরা মারা পড়ব।’
‘আমি কোনও ভুল করিনি। সেই মুহূর্তে ওটিই ছিল সঠিক সিদ্ধান্ত। আগেই বলেছি এই বাচ্চাটির মধ্যে আছে মানব-সত্তা এবং পিশাচ-সত্তা-দুইই। চার বছর বয়স পর্যন্ত একে নিয়ে খুব সমস্যা হয়নি। হ্যাঁ, হয়তো ছিল কিছু অস্বাভাবিকতা। কিন্তু সেসব বড় কোনও সমস্যা ছিল না। কিন্তু চার বছর বয়সে প্রথম জানল, সে অন্য কারও সন্তান। সেই দুর্বল মুহূর্তে জেগে উঠল তার পিশাচ-সত্তা। তার সাথে যোগাযোগ শুরু করল পিশাচ। তাকে বোঝাতে লাগল, চাইলে এই পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাধর প্রাণী হতে পারে সে। প্রায়ই ধ্যানমগ্ন হয়ে তার পিশাচ বাবার সাথে যোগাযোগ করত রাইয়ান। নানা ধরনের শক্তির চর্চাও হতো সেই মুহূর্তে। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছিল মারা গিয়েও পুনরায় বেঁচে ওঠার বিষয়টি। তার শারীরবৃত্তীয় কাজগুলো বন্ধ করে দিতে পারে রাইয়ান, আবার সচলও করতে পারে ধীরে- ধীরে। মুনি-ঋষিদের মধ্যে এই বিষয়টা নিয়ে প্রচলিত আছে অনেক গল্প। শরীরকে এমন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইয়োগা, ধ্যান, মেডিটেশন করতেন ঋষিরা। রাইয়ানও তার পিশাচ বাবার বশ্যতা স্বীকার করে ধ্যানের মাধ্যমে আত্মস্থ করেছিল এই বিষয়টি। আসলে আমরা তাড়িয়ে দিয়েছিলাম পিশাচকে। তাকে একবার তাড়ালে পুনরায় ফিরতে অনেক সমস্যা হয় তার। তাই কাজে লাগাচ্ছে সে রাইয়ানকে। ধীরে-ধীরে ওর মাধ্যমে ফিরে আসতে চায় সে।’
অন্যদিকে তাকিয়ে বলল আনোয়ার, ‘দেরি হয়ে গেছে। এখন আর সবকিছু আমাদের হাতে নেই। চাইলেও বাড়ি ছেড়ে যেতে পারব না আমি। এমন কী রাইয়ান না চাইলে এ বাসা থেকে বের হতে পারবেন না আপনিও।’ কথা শেষ করে নিজের ঘরে চলে এল আনোয়ার।
এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন রফিক সাদি। ধপাস করে সোফায় শুয়ে পড়লেন।
আনোয়ার বের হওয়া মাত্রই রফিক সাদির রুমে ঢুকল রাইয়ান, যেন এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল দাঁড়িয়ে। কিছু বলার চেষ্টা করলেন রফিক সাদি। কিন্তু মুখ দিয়ে বের হলো না কোনও শব্দ। এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল রাইয়ান। বাঘ যেমন শিকারের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, ওর দৃষ্টিও অনেকটা সেরকম। রফিক সাদির মনে হলো, রাইয়ানের চোখ দুটো জ্বলছে এবং গলা দিয়ে বের হচ্ছে ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ। ভয় পেয়ে চোখ নামিয়ে নিলেন রফিক সাদি। হঠাৎ লক্ষ করলেন, অসাড় হয়ে আসছে তাঁর হাত-পা। ঘর থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। মনে হচ্ছে, যেন প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে ভেতরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে কেউ। দুষ্টু হাসি রাইয়ানের মুখে।
দ্রুত ঘরের সাথে লাগোয়া বাথরুমে ঢুকলেন রফিক সাদি। ছেলেটার ওই ভয়ঙ্কর দৃষ্টি বেশিক্ষণ সহ্য করা সম্ভব নয়। রফিক সাদির মনে হলো, তিনি ছাড়াও আরও কেউ আছে বাথরুমে। কোনও বিশেষ কারণ ছাড়াই ঘুরে উঠল মাথাটা, পড়ে গেলেন তিনি বাথরুমের মেঝেতে। প্রচণ্ড ব্যথা পেলেন কোমরে, হাতে এবং পায়ে। চোখের সামনে দেখতে পেলেন রাইয়ানকে। একদিকে কাত হয়ে আছে তার মাথা, মুখ দিয়ে ঝরছে লালা। বহুদিন আগে তিনি ঝমঝম কুঠিতে দেখেছিলেন জয়নালের মধ্যে এমন ভঙ্গি। শাওয়ারটা ছেড়ে দিল কেউ। রফিক সাদির মনে হচ্ছে আর বাঁচবেন না তিনি।
চব্বিশ
রাইয়ানের ঘরে ঢুকল আনোয়ার। মেঝেতে বসে আছে রাইয়ান, মাথায় কালো একটা কাপড় বাঁধা। টকটকে লাল চোখ। একদিকে কাত হয়ে আছে মাথাটা। মুখ দিয়ে ঝরছে লালা। ডাকল আনোয়ার, ‘রাইয়ান।’
মাথাটা সোজা করে তাকাল রাইয়ান। চুষে নিল মুখের লালাটুকু। হিসহিসে গলায় বলল, ‘বল, কী বলবি?’
‘আমাকে তুই করে বলছ?’
‘তোর খুব আঁতে ঘা লেগেছে নাকি, জানোয়ার?’
‘তুমি কী চাও?’
‘আমি সবকিছু চাই এবং আমার বাবা আমাকে সবকিছু দেবেন।’
কে তোমার বাবা?’
‘মনে হচ্ছে তুই এখনও ফিডার খাস, কিছু বুঝতে পারছিস না?’
‘রফিক সাদিকে কেন বাথরুমে ফেলে দিলে? কেন আমাদের এই বাড়ি থেকে বের হতে দিচ্ছ না?’
‘আমি প্রতিশোধ নেব। খুব ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ।’ চোখে-মুখে ক্রোধের চিহ্ন ফুটে উঠল রাইয়ানের। ‘তোরা আমার এবং আমার বাবার সাথে যে অন্যায় করেছিস, তার বদলা আমাকে নিতেই হবে। রফিক সাদি, তোর বন্ধু শাহেদ চৌধুরী, নুযহাত এবং জানোয়ার, মানে তুই কাউকে ছাড়ব না।’
‘তুমি ভুল করছ, রাইয়ান। আমরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলাম, হত্যার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলাম।’ দৃঢ় কণ্ঠে আনোয়ার বলল, ‘তোমার বিরুদ্ধে কিছু করিনি। এমন কী তোমার মধ্যে ভয়ঙ্কর কিছু লুকিয়ে আছে জেনেও তোমাকে হত্যা করা হয়নি।’
‘হ্যাঁ, জানি। তুই আমাকে সুযোগ পেয়েও মেরে ফেলিসনি। এজন্য তোকে সবার শেষে মারব। আগে বাকিগুলোকে শেষ করব।’
‘শেষ করবে?’
‘হ্যাঁ। সবটুকু কষ্ট দিয়ে শেষ করব। তিলে-তিলে যন্ত্রণা দিয়ে শেষ করব।’
দাঁত বের করে হাসল রাইয়ান। অস্বাভাবিক লম্বা এবং সূচাল দাঁত দেখলে বুকটা আঁতকে উঠবে যে কারও।
‘আমার বাবা প্রায়ই স্বপ্নে আসেন। নানা দিকনির্দেশনা দেন। বাবার সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছি মৃত্যুকে। আমি দুইবার মরে, বেঁচে উঠেছি। এখন আমি এবং আমার বাবা না চাইলে কেউ মারতে পারবে না আমাকে।’ হাত উঁচু করে চিৎকার করে বলল রাইয়ান, ‘আমি নিষ্ঠুরতা দেখাতে চাই, মানুষকে কষ্ট দিতে চাই, সত্যিকারের পিশাচ হতে চাই। আমার বাবার মত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে চাই। আমি আর আমার বাবা শাসন করব পুরো পৃথিবী। আমার বাবা স্বপ্নে এবং ধ্যানে বারবার দেখা দেন। তিনি প্রতিনিয়ত পথ দেখাচ্ছেন আমাকে। গত দুই বছর ধরে ক্ষমতা বাড়িয়ে চলেছি আমি আমার।’
শীতল গলায় বলল আনোয়ার, ‘তোমার বাবা একটা নির্বোধ, ভীতু।’
‘কী বললি?’ বিকৃত হয়ে গেল রাইয়ানের মুখটা।
‘হ্যাঁ, ঠিকই বলেছি। তোমার বাবা মানুষের সামনে আসতে ভয় পায়, তার ক্ষমতা এখন শূন্যের কোঠায়। তাই তোমাকে কাজে লাগিয়ে আবার ক্ষমতাশালী হতে চায় সে।’
‘মিথ্যা! মিথ্যা বলছিস তুই! আমার বাবাকে তুই চিনি না!’ লাল হয়ে গেছে রাইয়ানের মুখ। দেখে মনে হলো পুড়ে গেছে মুখের খানিকটা অংশ। লাফ দিয়ে উঠেই আনোয়ারকে সজোরে চড় বসাল রাইয়ান। তাল সামলাতে না পেরে সামনের টেবিলে গিয়ে পড়ল আনোয়ার। মেঝেতে পড়ে গেল ফুলদানিটা। কয়েক মুহূর্ত চোখে-মুখে অন্ধকার দেখল আনোয়ার। রক্তের লোনা স্বাদ পেল মুখের ভেতর। মুখে বরফ ঘষছে আনোয়ার। বেশ ফুলে উঠেছে মুখটা। এদিকে শয্যাশায়ী রফিক সাদিও। তার বন্ধু ডিবি পুলিস অফিসার শাহেদকে ফোন দিল আনোয়ার। আগেরবার অনেক সাহায্য করেছিল শাহেদ, এবারও প্রয়োজন তার সাহায্য।
ফোনটা ধরল না শাহেদ, ধরল ওর মা। তিনি কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বললেন, ‘গতকাল অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে শাহেদের। শরীরের চারটা হাড় ভেঙেছে। মাথায় ও পেয়েছে গুরুতর আঘাত।’
শ্বাসটা আটকে রেখে বলল আনোয়ার, ‘কীভাবে হলো অ্যাক্সিডেন্ট?’
‘আমরা কিছুই জানি না। গতকাল শাহেদকে গুলশান দুইয়ের গোল চত্বরের সামনে পড়ে থাকতে দেখে পুলিস। তারপর নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে।’
আণ্টিকে সান্ত্বনা দিয়ে ফোন রেখে বিড়বিড় করে বলল আনোয়ার, ‘রাইয়ান!’ এরপর যোগাযোগ করতে চাইল কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে। কিন্তু ডেড হয়ে গেছে ল্যাণ্ড ফোন। কাজ করল না মোবাইল ফোনও।
সাধনা – ২৫
পঁচিশ
শারীরিক এবং মানসিকভাবে খুব ভেঙে পড়েছেন রফিক সাদি। এদিকে বেশিরভাগ সময় নিজের রুমে দরজা বন্ধ করে রাখছে রাইয়ান।
রফিক সাদির ঘরে ঢুকে চমকে উঠল আনোয়ার। কাঁপা গলায় বলল, ‘আপনার মুখে এত আঁচড়ের চিহ্ন কীসের?’
‘কাল রাতে দুঃস্বপ্ন দেখেছিলাম।’
‘কী দুঃস্বপ্ন?’
‘দেখি, প্রবল আক্রোশে বড়-বড় নখ দিয়ে আমার মুখে আঁচড় দিচ্ছে একটা ভয়ঙ্কর প্রাণী। আর বলছে, ‘আমি তোকে মেরে ফেলব, অনেক কষ্ট দিয়ে মারব।’ ঘুম ভাঙার পর দেখলাম মুখের বিভিন্ন জায়গা দিয়ে রক্ত বের হচ্ছে।’ কেঁদে ফেললেন রফিক সাদি।
বাবার পাশে বসে আছে নুযহাত। আনোয়ারের দিকে তাকিয়ে বলল, ‘এসব কী হচ্ছে, একটু বুঝিয়ে বলবেন? আমি আজ বাসা থেকে বের হওয়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু মনে হলো অদৃশ্য কেউ শক্ত করে চেপে ধরেছে আমার হাত। এমন কী খুলতে পারলাম না গেটের তালাটাও। ডেড হয়ে পড়ে আছে সব মোবাইল ফোন। এদিকে বাবার এ অবস্থা! রীতিমত ভয় লাগছে আমার!’
সহজে আর এই বাড়ি থেকে বেরোতে পারবে না, বুঝে গেছে আনোয়ার। বাধা দেবে রাইয়ান। সে ক্ষমতা তার আছে। রফিক সাদির দিকে তাকিয়ে বলল আনোয়ার, ‘আমার মনে হয়, সব খুলে বলা উচিত নুযহাতকে।’
হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না রফিক সাদি। নুযহাতকে ধীরে-ধীরে সব খুলে বলতে লাগল আনোয়ার। শুনছে নুযহাত, বারবার কেঁপে উঠছে তার শরীর আনোয়ারের সব কথা শেষ হলেও যেন জগতে ফিরতে পারল না মেয়েটা। কিছুক্ষণ পর ধরে রাখতে পারল না চোখের পানি। কাতর গলায় বলল, ‘বাবা, তুমি কেন মিথ্যা বলেছিলে আমাকে? তুমি বলেছিলে মারা গেছে আমার সন্তান। তখন মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ছিলাম, সেই সুযোগে উল্টাপাল্টা বুঝিয়েছিলে তুমি আমাকে।’
‘মা, যা করেছি, তোর ভালর জন্যই করেছি। এই ছেলেটা সাক্ষাৎ পশু।’
‘খবরদার, বাবা! আমার ছেলেকে নিয়ে খারাপ কিছু বলবে না!’
‘যে অল্প বয়স থেকেই মানুষকে ভয়ানকভাবে কষ্ট দেয়, যে পিশাচের কথা অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলে, যে মরে গিয়ে আবারও জীবিত হয়, তাকে তুই ছেলে বলছিস?’
‘আমার ছেলে কোনও পশু নয়, সে পড়েছে একটা পশুর কবলে।’
মাথা নেড়ে বলল আনোয়ার, ‘আপনার কথা অনেকাংশে ঠিক। মানুষের শক্তি পিশাচের চেয়ে অনেক বেশি। দেখুন, চার বছর বয়স পর্যন্ত কোনও ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটায়নি রাইয়ান। কারণ ততদিন পর্যন্ত সে নিজেকে ভেবে এসেছে মানুষ। কিন্তু যখনই জানল, মুবিন চৌধুরী, মরিয়ম বেগম তার মা-বাবা নয়, তখনই সুযোগের সদ্ব্যবহার করল পিশাচটা। নানাভাবে প্রভাবিত করতে লাগল রাইয়ানকে, তার পিশাচ-সত্তাকে জাগিয়ে তুলল পুরোপুরি।’
ভাঙা গলায় বলল নুযহাত, ‘আমি অত কিছু বুঝি না, আমি আমার ছেলের কাছে যাব।’
‘আপনার কথা ভাল লেগেছে আমার,’ আনোয়ার বলল, ‘রাইয়ান অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। মন্ত্র, তাবিজ বা এ ধরনের অন্য কিছু কোনও ফল বয়ে আনবে না। বাঁচতে চাইলে আমাদের একটাই উপায় আছে।’
‘কী উপায়?’
‘জাগিয়ে তুলতে হবে রাইয়ানের মানবীয় সত্তাকে।’
সেটা কীভাবে সম্ভব?’
‘রাইয়ানকে উজাড় করে দিতে হবে আপনার সব মমতা। সে আঘাত করলেও, খারাপ কথা বললেও আমাদেরকে সহ্য করতে হবে। সে যতই প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মত কথা বলুক না কেন, তার মধ্যে আছে শিশুর মন, সেটা জাগিয়ে তুলতে হবে। সেক্ষেত্রে রাইয়ানকে আর কোনও কাজে লাগাতে পারবে না পিশাচটা।’
উঠে দাঁড়িয়ে বলল নুযহাত, ‘আমি আমার ছেলেকে মমতা দেব না কেন? ওকে আমি বুকের মধ্যে আগলে রাখব।’
‘কাজটা অনেক কঠিন। তবু আমাদের চেষ্টা করতে হবে।’
ছাব্বিশ
রাইয়ানের হাতে একটা সাদা বিড়াল। হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ওটার মাথায়। আনোয়ার এবং নুযহাতকে দেখে ফুটে উঠল তার কপালের রগ। ক্রোধমাখা কণ্ঠে বলল, ‘তোরা আমার কাছে এসেছিস কেন?’
‘আমি তোমার মা, রাইয়ান, বাবা,’ হাত বাড়িয়ে বলল নুযহাত। ‘হারামজাদী, চুপ কর! আমার কোনও মা নেই!’
নিজের আবেগ সামলে অনেক কষ্টে বলল নুযহাত, ‘আমি তোমার মা। আমি তোমাকে গর্ভে ধরেছি।’
‘বাঁচার জন্য আমার সাথে আলগা পিরিত করতে এসেছিস? বাঁচবি না, বাঁচবি না, তোরা কেউ বাঁচবি না!’
‘তুমি চাইলে আমাকে মেরে ফেলো, কোনও সমস্যা নেই। সন্তানের জন্য জীবন দিতে মা সবসময় প্রস্তুত।’
‘আয়! তোর হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে নিই! দেখি তুই কত ভালবাসিস আমাকে!’
‘ছি, বাবা। বাজে কথা বলতে হয় না।’
একটানা অনেকগুলো অশ্লীল গালি দিল রাইয়ান। কানে হাত দিল নুযহাত। এখানেই থেমে থাকল না রাইয়ান। এক টানে আলাদা করে ফেলল বিড়ালটার ধড় থেকে মাথা। রক্ত মেখে হয়ে উঠল দেহ রঞ্জিত। জোরে হাসতে লাগল রাইয়ান। রক্ত তার ভাল লাগে।
সন্তানের জন্য সম্ভবত সবকিছু করতে পারেন মা। নানাভাবে রাইয়ানের কাছে যাওয়ার চেষ্টা করল নুযহাত, বোঝানোর চেষ্টা করল তাকে। একদিন পার হলো, দু’দিন পার হলো, দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল এক সপ্তাহ। তাকে আঘাত করল রাইয়ান, অশ্লীল কথা বলল, কখনও দিল ভয়ঙ্কর কষ্ট, তবু লক্ষ্য থেকে এক চুল পিছু হটল না নুযহাত। কারণ সে জানে, তার ছেলেকে ভাল করার একমাত্র উপায় মমতা ঢেলে দেয়া।
রাইয়ানকে বোঝানোর চেষ্টা করল আনোয়ারও। বলল, ‘ক্ষমতাই সবকিছুর শেষ কথা নয়। তোমাকে মিথ্যা শিখিয়েছে পিশাচ। তোমার মাধ্যমে এই পৃথিবীতে রাজত্ব করতে চায় সে।’
‘আনোয়ার, মেরে ফেলার সময় হয়েছে তোকে। সবটুকু কষ্ট দিয়ে তোকে মারব আমি। তোর জন্য বহুদূরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছেন আমার বাবা।’
‘রাইয়ান, তুমি বুদ্ধিমান ছেলে, পুরো বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করো।
‘তুই তো মন্ত্র-তন্ত্র করে হারিয়ে দিয়েছিলি আমার বাবাকে। এবার পারলে মন্ত্র পাঠ করে তাড়িয়ে দে আমাকে!’
‘তুমি মানুষ, পিশাচকে তাড়ানোর মন্ত্র তোমার জন্য কাজ করবে না। মন্ত্র দিয়ে তাড়ানো যায় না মানুষকে।’
‘আমি মানুষ নই, পিশাচ। আমি পিশাচের সন্তান। আমার বাবা আমাকে অনেক ভালবাসেন। আমি আমার বাবাকে ভালবাসি।’
‘ঠিক আছে, চলো, হয়ে যাক পরীক্ষা।’
‘কী পরীক্ষা, আনোয়ার?’
‘তোমার বাবা যদি তোমাকে এতই ভালবাসে, তবে তাকে ডাকো। তার সাহস থাকলে এখানে আসুক। এসে বলুক, তুমি তার সন্তান।’
‘তুই কি ভেবেছিস আমার বাবা আসবেন না? আমার বাবা ‘অবশ্যই আসবেন। আর আমার বাবা এলে ছিঁড়ে নেবেন তোর কলিজা। তোকে খণ্ড-খণ্ড করে প্রতিশোধ নেবেন।’
‘না, রাইয়ান, সে আসবে না। মানুষ শ্রেষ্ঠ, পিশাচ অনেক নিম্নশ্রেণীর সত্তা। সে আমার সামনে আসার সাহস পাবে না। সে আমাকে ভয় পায়। কারণ, আগেরবার আমার কাছে পরাজিত হয়েছিল।’
চোখ বন্ধ করে তার বাবাকে ডাকতে থাকল রাইয়ান। বুকের মধ্যে কেউ যেন ঢাকের মত শব্দ করছে আনোয়ারের। সে অনেক বড় একটা ঝুঁকি নিয়েছে। এক ধরনের জুয়া খেলেছে। সত্যি যদি চলে আসে পিশাচটা, অনায়াসেই দু’জন মিলে মেরে ফেলবে ওকে।
বেশ কিছুক্ষণ পেরিয়ে গেল, চোখ বন্ধ করে আছে আনোয়ারও। চেষ্টা করছে মনকে শান্ত করতে। পুরো ঘরে পিনপতন নীরবতা। কয়েক মিনিট পর চোখ মেলে তাকাল রাইয়ান। আনোয়ার লক্ষ করল, কেমন যেন একটা হতভম্ব ভাব ফুটে উঠেছে রাইয়ানের চোখে।
‘আমার বাবা এখন আসবেন না,’ রাইয়ান বলল, ‘তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন তোমাকে মেরে ফেলতে।’ রাইয়ান আবারও তুমি করে বলা শুরু করেছে আনোয়ারকে, এটা ভাল লক্ষণ।
আনোয়ার বলল, ‘রাইয়ান, ওই পিশাচ নিজ স্বার্থে তোমাকে ভুল জিনিস শিখিয়েছে। এতদিন তার কথা বিশ্বাস করেছ। এবার আমাদের কথা বিশ্বাস করে দেখো। মানুষ হয়ে মানুষকে হত্যা করা যায় না। আমি তোমাকে হত্যা করতে পারিনি। আমি জানি, তুমিও আমাকে হত্যা করতে পারবে না।’
নুযহাত বলল, ‘বাবা, আমার বুকে আয়।’
কয়েক কদম পিছিয়ে গেল রাইয়ান। চিৎকার করে বলল, ‘না-না! আমার কাছে আসবে না! আমি সব ধ্বংস করে দেব! সব!’ বলতে-বলতে যেন ঝড় উঠল পুরো বাড়িতে। তুলোর মত কাঁপতে লাগল সবকিছু। তাল সামলাতে না পেরে মেঝেতে পড়ে গেল নুযহাত ও আনোয়ার। কিছু একটা আঘাত করল ওদের দু’জনকে, প্রচণ্ড গতিতে। একটা অদৃশ্য হাত গলা চেপে ধরেছে নুযহাতের কোনওভাবেই তার নিস্তার নেই। তবু বলার চেষ্টা করল নুযহাত, ‘বাবা রে, আমি মনে হয় মরে যাব! আমার কাছে আয়, একবার তোর মাথায় হাত বুলিয়ে দিই!’
আনোয়ার চিৎকার করে বলল, ‘রাইয়ান, ভুল করছ, মানুষকে বিশ্বাস করো, পিশাচকে নয়। ভুল করছ, রাইয়ান। ভুল…’
অপ্রকৃতিস্থের মত নিজের মাথা ঝাঁকাতে লাগল রাইয়ান। মনে হচ্ছে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে তার। ঘরের মধ্যে বেগ বাড়তে থাকে বাতাসের। ধুপ-ধুপ শব্দ করে এ-মাথা ও-মাথা দৌড়াচ্ছে কেউ।
এখনও সেই হাত চেপে ধরে রেখেছে নুযহাতের গলা। বহুকষ্টে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল সে, ‘রাইয়ান…আমার ছেলে…আমার ছেলে! আমি তার মা!’ বলতে-বলতে শরীর এলিয়ে পড়ল নুযহাতের। মনে হলো সে আর বেঁচে নেই। এমন সময় হুট করেই শান্ত হয়ে এল বাড়ির পরিবেশটা। কেমন যেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রাইয়ান।
আনোয়ার বলল, ‘রাইয়ান, তোমার মা মারা যাচ্ছে! বাইরে যেতে দাও আমাদের! হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে তাকে! আমাদের বিশ্বাস করো!’
কিছু না বলে দৌড়ে বাসার বাইরে চলে গেল রাইয়ান।
দেরি না করে নুযহাতকে হাসপাতালে নিয়ে গেল আনোয়ার।
সাতাশ
প্রাণে বেঁচে গেছে নুযহাত। তবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার শ্বাসনালী। এ ছাড়া, টানা এক সপ্তাহ ক্রমাগত শারীরিক আঘাতে বিপর্যস্ত। বেশ কিছুদিন বিশ্রাম ও নিয়ম মেনে চলতে হবে। পাঁচদিন পরে হাসপাতাল থেকে রিলিজ দেয়া হলো নুযহাতকে। আগের চেয়ে অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন রফিক সাদিও। মেয়েকে নিয়ে দ্রুত কানাডা ফিরতে চাইছেন তিনি।
কিন্তু রাজি হচ্ছে না নুযহাত, ছেলেকে রেখে কানাডা যেতে রাজি নয়।
বাসা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল রাইয়ান, এরপর আর কোনও খোঁজ নেই তার। নিজের বাসায় ফিরে গেছে আনোয়ার। প্রায় প্রতিদিনই রফিক সাদির বাসায় আসে সে। কারও মুখেই কোনও কথা থাকে না, গম্ভীর মুখে বসে থাকে সবাই। দিন এবং রাতের বেশ খানিকটা সময় রাইয়ানকে খুঁজে বেড়ায় আনোয়ার। রহস্যের কথা বাদ দিলেও এক ধরনের মায়া অনুভব করে ও বাচ্চাটার প্রতি।
সারাক্ষণ কাঁদে নুযহাত
মেয়ের ক্রমাগত কান্না কষ্ট দিচ্ছে রফিক সাদিকেও। মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। কাঁদতে-কাঁদতে বলে নুযহাত, ‘বাবা, কোথায় হারিয়ে গেল আমার ছেলে?’
বিড়বিড় করে বলেন রফিক সাদি, ‘সব ঠিক হয়ে যাবে, মা। সব ঠিক হয়ে যাবে।’
‘আমার ছেলে কি ফিরে আসবে না, বাবা?’
‘নিশ্চয়ই ফিরে আসবে, মা।’
‘ওকে তুমি ভুল বুঝো না, বাবা। ছোট বাচ্চা তো।’
.
যেমন হুট করে চলে গিয়েছিল রাইয়ান, তেমনি হুট করেই ফিরল। এই কয়েক দিনে শুকিয়ে অর্ধেক হয়ে গেছে। পোশাক বিবর্ণ। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় রক্ত শুকিয়ে কালো। নির্বিকার ভঙ্গিতে রফিক সাদির বাসায় ঢুকে পড়ল সে। রাইয়ানকে পেয়ে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করল নুযহাত। কিন্তু এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রাইয়ান। এক দৌড়ে চলে গেল নিজের রুমে। রাইয়ান ফিরে আসার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি করে রাফিক সাদির বাড়িতে এল আনোয়ার।
সারাদিন দরজা বন্ধ করে থাকল রাইয়ান। দরজা খুলল বিকেল মিলিয়ে যাওয়ার পর। ভালভাবে গোসল করে, পরেছে নতুন পোশাক। ওকে দেখে মনে হলো না, ওর মধ্যে অশুভ কিছু আছে। আনোয়ারের দিকে তাকিয়ে বলল রাইয়ান, ‘তুমি ঠিকই বলেছিলে। মানুষই শ্রেষ্ঠ। `মাথাটা নিচু করে নিল ও। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। ‘এই ক’দিনে আমি আমার বাবাকে চিনে ফেলেছি। সে আমার কষ্টের সময় আমাকে এতটুকু সাহায্য করেনি। তার মনে হিংসা, ক্রোধ, লোভ আর মিথ্যার বাস। সেখানে মমতা বলে কিছু নেই। পুরো পৃথিবীতে রাজত্ব করতে চায় আমার মাধ্যমে।’
বড় করে দম নিয়ে রাইয়ান বলল, ‘তোমাদের মাঝে এসে বদলাতে বাধ্য হয়েছি। সেই পিশাচকে জানিয়ে দিয়েছি, আমি মানুষ হয়েই বাঁচতে চাই, পিশাচ হয়ে নয়। আমার এ মনোভাব জেনে আমাকে পরিত্যাগ করেছে সে।’
স্বস্তির রেখা দেখা দিল আনোয়ার, নুযহাতের মুখে। দৌড়ে গিয়ে রাইয়ানকে জড়িয়ে ধরল ওর মা। কপালে চুমু খেয়ে বলল, ‘আমি তোকে কানাডা নিয়ে যাব, বাবা। তুই সব ভুলে যাবি। আমি তোকে সবসময় বুকে জড়িয়ে ধরে রাখব।’
‘না।’
‘মানে?’
‘আমি পিশাচের বশ্যতা স্বীকার করেছি, এক অর্থে তার সাধনা করেছি। তার মাধ্যমে মৃত থেকে হয়েছি জীবিত। এখন আমাকে পরিত্যাগ করেছে সে। এর মানে কি জানো?’
‘কী?’
‘আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আমি মারা যাব।’
‘মানে?’
‘যদি জীবিত-মৃতের এই খেলাটা না খেলতাম, যদি সবকিছু পিশাচের উদ্দেশে সঁপে না দিতাম, তবে আজ তোমাদের মাঝে বেঁচে থাকতাম।
‘তোমার কিছু হবে না, রাইয়ান,’ জোর গলায় বলল আনোয়ার, ‘আমরা তোমার সাথে আছি।’
মৃদু হেসে রাইয়ান বলল, ‘দেখছ না আমার শরীর কেমন খারাপ হয়ে গেছে? এবার সত্যিকারভাবে মরব। আর কোনও শক্তি আমাকে বাঁচাতে পারবে না।’
‘এসব কী বলছিস, বাবা? কেউ তোকে মারতে পারবে না! কেউ না!’ ডুকরে কেঁদে উঠল নুযহাত।
আনোয়ার বলল, ‘রাইয়ান, তোমার বেঁচে থাকাটা জরুরি। তুমি আবার পিশাচের বশ্যতা স্বীকার করো। তাতে অন্তত বাঁচবে। আমরা অন্যভাবে মোকাবেলা করব পিশাচের।’
‘না,’ আস্তে করে মাথা নাড়ল রাইয়ান। ‘পিশাচের অধীনে বাঁচার চেয়ে স্বাধীন মানুষ হয়ে মরা অনেক ভাল। আমি আর পিশাচের আরাধনা করব না। একটু বিরতি নিয়ে অনুরোধের সুরে বলল রাইয়ান, ‘তোমরা একটা কাজ করবে?’
‘বলো,’ নরম সুরে বলল আনোয়ার।
‘তোমরা মাঝে-মাঝে যাবে আমার কবরের কাছে। যেমন মানুষ মানুষের জন্য স্রষ্টার কাছে দোয়া করে, আমার জন্যে তাই করবে তোমরাও।’ আনোয়ারের মুখ থেকে কোনও কথা বের হলো না। কান্নায় ভেঙে পড়ল নুযহাত। পরম মমতায় রাইয়ানের কপালে হাত রাখলেন রফিক সাদি।
শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে রাইয়ানের। জীবনে প্রথমবারের মত নুযহাতকে ‘মা’ বলে ডাকল। ‘মা, এই ছবিটা তোমার জন্য।’ পকেট থেকে বের করে একটা ফোটো নুযহাতের হাতে দিল রাইয়ান।
শুরু হয়েছে ওর শরীরে তীব্র খিঁচুনি। নুযহাত শক্ত করে ওকে জড়িয়ে ধরলেও এতটুকু কমল না ওর কাঁপুনি। ক্রমশ কালো হয়ে গেল রাইয়ান। মনে হলো, শরীরের মধ্য দিয়ে নড়াচড়া করছে কিছু। উথাল-পাতাল হাওয়া যেন ওকে উড়িয়ে নেবে। একটু পর থামল সব, নিথর হয়ে রইল রাইয়ান।
ওর দেয়া ছবিটা নুযহাতের কাছ থেকে নিল আনোয়ার।
ছবিতে তার মায়ের কোলে শুয়ে আছে একটা বাচ্চা। ছবির নিচে লিখেছে রাইয়ান, ‘মা, এত দেরি করে এলে কেন?’
মুহূর্তেই চোখের সামনে সবকিছু ঝাপসা হয়ে গেল আনোয়ারের। মনে পড়ল ওর নিজের মা-র কথা।
***