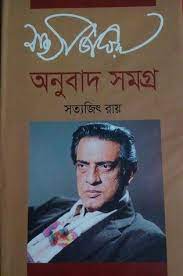- বইয়ের নামঃ সত্যজিৎ রায়ের অনুবাদ
- লেখকের নামঃ সত্যজিৎ রায়
- বিভাগসমূহঃ সমগ্র
আবার মোল্লা নাসিরুদ্দিন
১.
রাজামশাই একদিন নাসিরুদ্দিনকে ডেকে বললেন, বনে গিয়ে ভাল্লুক মেরে আনো।
নাসিরুদ্দিন রাজার আদেশ অমান্য করে কী করে? অগত্যা তাকে যেতেই হল।
বন থেকে ফেরার পর একজন তাকে জিজ্ঞেস করলে, কেমন হল শিকার, মোল্লাসাহেব?
চমৎকার, বললে নাসিরুদ্দিন।
কটা ভাল্লুক মারলেন?
একটিও না।
বটে? কটাকে ধাওয়া করলেন?
একটিও না।
সে কী। কটা দেখলেন?
একটিও না।
তা হলে চমৎকারটা হল কী করে?
ভাল্লুক শিকার করতে গিয়ে সে জানোয়ারের দেখা না পাওয়ার চেয়ে চমৎকার আর কী হতে পারে?
.
২.
এক পড়শি এসেছে নাসিরুদ্দিনের কাছে এক আর্জি নিয়ে।
মোল্লাসাহেব, আপনার গাধাটা যদি কিছুদিনের জন্য ধার দেন তো বড় উপকার হয়।
মাফ করবেন, বললে নাসিরুদ্দিন, ওটা আরেকজনকে ধার দিয়েছি।
কথাটা বলামাত্র বাড়ির পিছন থেকে গাধা ডেকে উঠে তার অস্তিত্ব জানান দিয়ে দিল।
সে কী মোল্লাসাহেব, ওটা আপনারই গাধার ডাক শুনলাম না?
নাসিরুদ্দিন মহারাগে লোকটার মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেওয়ার সময় বললে, আমার কথার চেয়ে আমার গাধার ডাককে যে বেশি বিশ্বাস করে, তাকে কোনওমতেই গাধা ধার দেওয়া চলে না।
.
৩.
এক বেকুবের শখ হয়েছে সে পণ্ডিত হবে। সে মনে মনে ভাবলে মোল্লার তো নামডাক আছে পণ্ডিত হিসেবে, তার কাছেই যাওয়া যাক, যদি কিছু শেখা যায়।
অনেকখানি পথ পাহাড় ভেঙে উঠে সে খুঁজে পেলে নাসিরুদ্দিনের বাসস্থান। ঢোকবার আগে জানলা দিয়ে দেখলে মোল্লাসাহেব ঘরের এককোণে ধুনুচির সামনে বসে নিজের দু হাতের তেলো মুখের সামনে ধরে তাতে ফুঁ দিচ্ছে।
ঘরে ঢুকে বেকুব প্রথমেই হাতে ফুঁ দেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে। ফুঁ দিয়ে হাত গরম করছিলাম, বলে নাসিরুদ্দিন চুপ করলে। বেকুব ভাবলে, একটা জিনিস তো জানা গেল। আর কিছু জানা যাবে কি?
কিছুক্ষণ পরে নাসিরুদ্দিনের গিন্নি দুবাটি গরম দুধ এনে কর্তা আর অতিথির সামনে রাখলেন। নাসিরুদ্দিন তক্ষুনি দুধে ফুঁ দিতে শুরু করলে।
এবার বেকুব সম্ভ্রমের সঙ্গে শুধোলে, হে গুরু, এবারে ফুঁ দেবার কারণটা কী?
দুধ ঠাণ্ডা করা, বললে নাসিরুদ্দিন।
বেকুব বিদায় নিলেন। যে লোক বলে ফুঁ দিয়ে জিনিস গরম হয়, আবার ঠাণ্ডাও হয়, তার কাছ থেকে জ্ঞানলাভের কোনও আশা আছে কি?
.
৪.
মোল্লা এখন কাজি, সে আদালতে বসে। একদিন এক বুড়ি তার কাছে এসে বললে, আমি বড়ই গরিব। আমার ছেলেকে নিয়ে বড় ফ্যাসাদে পড়েছি কাজিসাহেব। সে মুঠো মুঠো চিনি খায়, তাকে আর চিনি জুগিয়ে কুল পাচ্ছি না। আপনি হুকুম দিয়ে তার চিনি খাওয়া বন্ধ করুন। সে আমার কথা শোনে না।
মোল্লা একটু ভেবে বললে, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। এক হপ্তা পরে এসো, আমি একটু বিবেচনা করে তারপর এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব।
বুড়ি হুকুমমতো এক হপ্তা পরে আবার এসে হাজির! মোল্লা তাকে দেখে মাথা নাড়লে।–এ বড় জটিল মামলা। আরও এক হপ্তা সময় দিতে হবে আমাকে।
আরও সাতদিন পরেও সেই একই কথা। অবশেষে ঠিক এক মাস পরে মোল্লা বুড়িকে বললে, কই, ডাকো তোমার ছেলেকে।
ছেলেটি আসতেই মোল্লা তাকে হুঙ্কার দিয়ে বললে, দিনে আধ ছটাকের বেশি চিনি খাওয়া চলবে। যাও।
বুড়ি মোল্লাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললে, একটা কথা জিজ্ঞেস করার ছিল, কাজিসাহেব।
বলো।
এই নিয়ে চারবার ডাকলেন কেন আমাকে? এর অনেক আগেই তো আপনি এ হুকুম দিতে পারতেন।
তোমার ছেলেকে হুকুম দেবার আগে আমার নিজের চিনি খাওয়ার অভ্যেস কমাতে হবে তো! বললে নাসিরুদ্দিন।
.
৫.
রাস্তার কয়েকটি ছোঁকরা ফন্দি করেছে তারা মোল্লাসাহেবের জুতোজোড়া হাত করবে। একটা লম্বা গাছের দিকে দেখিয়ে তারা মোল্লাসাহেবকে বললে, ওই যে গাছ দেখছেন, ওটায় চড়ার সাধ্যি কারুর নেই।
আমার আছে, বলে মোল্লাসাহেব জুতোজাড়া পা থেকে না খুলেই গাছটায় চড়তে শুরু করলেন। বেগতিক দেখে ছেলেরা চেঁচিয়ে বলল, ও মোল্লাসাহেব, ওই গাছে আপনার জুতো কোনও কাজে লাগবে কি?
মোল্লাসাহেব গাছের উপর থেকে জবাব দিলেন, গাছের মাথায় যে রাস্তা নেই তা কে বলতে পারে?
.
৬.
নাসিরুদ্দিন বাজারে গিয়ে এক নিলামদারের হাতে তার গাধাটিকে তুলে দিলে। সেটাকে দিয়ে আর কাজ চলে না, তাই একটা নতুন গাধা কেনা দরকার।
আর পাঁচরকম জিনিস পাচার হয়ে যাবার পর গাধা যখন নিলামে উঠল, নাসিরুদ্দিন তখন কাছাকাছির মধ্যেই রয়েছে। নিলামদার হাঁক দিলে, এবার দেখুন এই অসামান্য, অতুলনীয় গাধা। পাঁচ স্বর্ণমুদ্রা কে দেবেন এর জন্য? মাত্র পাঁচ স্বর্ণমুদ্রা!
এক চাষা হাত তুললে। দর এত কম দেখে মোল্লাসাহেব নিজেই হেঁকে বসলেন, ছয় স্বর্ণমুদ্রা।
ওদিকে অন্য লোকেও ডাকতে শুরু করেছে, আর নিলামদারও গাধার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। দর যত বাড়ে ততই বাড়ে গুণের ফিরিস্তি।
চাষা ও মোল্লাসাহেবের মধ্যে ডাকাডাকিতে গাধার দাম চড়ে চল্লিশ স্বর্ণমুদ্রায় পৌঁছে শেষটায় মোল্লাসাহেবেরই জিত হল। গাধার আসল দাম ছিল বিশ স্বর্ণমুদ্রা, অর্থাৎ লোকসান হল দ্বিগুণ।
কিন্তু তাতে কী এসে গেল? যে গাধার এত গুণ, বললে মোল্লাসাহেব, তার জন্য চল্লিশ স্বর্ণমুদ্রা তো জলের দর।
.
৭.
নাসিরুদ্দিন মওকা বুঝে একজনের সবজির বাগানে গিয়ে হাতের সামনে যা পায় থলেতে ভরতে শুরু করেছে।
এদিকে মালিক এসে পড়েছেন। কাণ্ড দেখে তিনি হন্তদন্ত নাসিরুদ্দিনের দিকে ছুটে এসে বললেন, ব্যাপারটা কী?
নাসিরুদ্দিন বললে, ঝড়ে উড়িয়ে এনে ফেলেছে আমায় এখানে।
আর খেতের সবজিগুলোকে উপড়ে ফেলল কে?
ওড়ার পথে ওগুলিকে খামচে ধরে তবে তো রক্ষা পেলাম।
আর সবজিগুলো থলের মধ্যে গেল কী করে?
সেই প্রশ্নই তো আমাকেও চিন্তায় ফেলেছিল, এমন সময় আপনি এসে পড়লেন।
.
৮.
মোল্লাগিন্নি মাঝরাত্তিরে নাসিরুদ্দিনের ঘুম ভাঙিয়ে বললেন, ব্যাপার কী? চশমা পরে ঘুমোচ্ছ কেন?
মোল্লা নতুন চশমা নিয়েছে। খাপ্পা হয়ে বললে, চোখে চালশে পড়েছে, চশমা ছাড়া স্বপ্ন দেখব কী করে?
.
৯.
থলেতে একঝুড়ি ডিম লুকিয়ে নিয়ে নাসিরুদ্দিন চলেছে ভিনদেশে। সীমানায় পৌঁছতে শুল্ক বিভাগের লোক তাকে ধরলে। নাসিরুদ্দিন জানে ডিম চালান নিষিদ্ধ।
মিথ্যে বললে মৃত্যুদণ্ড বললে শুল্ক বিভাগের লোক। তোমার থলেতে কী আছে বলো।
প্রথম অবস্থার কিছু মুরগি, বললে মোল্লাসাহেব।
হুম–সমস্যার কথা। মুরগি চালান নিষিদ্ধ কিনা খোঁজ নিতে হবে, তারপর ব্যাপারটার মীমাংসা হবে। ততদিন এ থলি রইল আমাদের জিম্মায়। ভয় নেই, তোমার মুরগিকে উপোস রাখব না আমরা।
কিন্তু আমার মুরগির জাত যে একটু আলাদা, বললে নাসিরুদ্দিন।
কীরকম।
আপনারা তো শুনেছেন অবহেলার দরুন মুরগির অকাল বার্ধক্য আসে।
তা শুনেছি বটে!
আমার মুরগিকে ফেলে রাখলে সেগুলো অকালে শিশু হয়ে যায়!
শিশু মানে?
একেবারে শিশু, বললে নাসিরুদ্দিন, যাকে বলে ডিম।
.
১০.
মোল্লা মসজিদে গিয়ে বসেছে, তার জোব্বাটা কিঞ্চিৎ খাটো দেখে তার পিছনের লোক সেটাকে টেনে খানিকটা নামিয়ে দিলে। মোল্লা তৎক্ষণাৎ তার সামনের লোকের জোব্বাটা ধরে নীচের দিকে দিলে এক টান। তাতে লোকটি পিছন ফিরে চোখ রাঙিয়ে বললে, এটা কী হচ্ছে?
মোল্লা বললে, এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারে আমার পিছনের লোক।
.
১১.
কারও মৃত্যু হলে শোক জানানোর জন্য কালো পোশাক পরে মোল্লার দেশের লোকেরা। মোল্লাকে সেই পোশাকে হাঁটতে দেখে একজন জিজ্ঞেস করলে, কেউ মরল নাকি, মোল্লাসাহেব?
সাবধানের মার নেই, বললে মোল্লাসাহেব, কোথায় কখন কে মরছে তা কি কেউ বলতে পারে?
.
১২.
নাসিরুদ্দিন রাজাকে একটা সুখবর দেবে, তাই অনেক কসরৎ করে রাজসভায় গিয়ে হাজির হয়েছে। রাজা খবর শুনে খুশি হয়ে বললেন, কী বকশিশ চাও বলো।
পঞ্চাশ ঘা চাবুক, বললে নাসিরুদ্দিন।
রাজা অবাক! তবে নাসিরুদ্দিন যে মশকরা করছে না সেটা তার মুখ দেখেই বোঝা যায়। হুকুম হল পঞ্চাশ ঘা চাবুকের।
পঁচিশ ঘায়ের পর নাসিরুদ্দিন বললে, থামো!
চাবুক থামল। বাকি পঁচিশ ঘা পাবে আমার অংশীদার, বললে নাসিরুদ্দিন। রাজপেয়াদা আমার সঙ্গে কড়ার করেছিল সুখবর পেয়ে রাজা বকশিশ দিলে তার অর্ধেক তাকে দিতে হবে।
সন্দেশ, মাঘ ১৩৮৭
আর এক দফা মোল্লা নাসিরুদ্দিন
১.
নাসিরুদ্দিন রাস্তা দিয়ে হাঁটছে, পাশে ফুলে ফলে ভরা বাগিচা দেখে তার মধ্যে গিয়ে ঢুকল। প্রকৃতির শোভাও উপভোগ করা হবে, শর্টকাটও হবে।
কিছুদূর যেতে না যেতেই নাসিরুদ্দিন এক গর্তের মধ্যে পড়ল, আর পড়তেই তার মনে এক চিন্তার উদয় হল।
ভাগ্যে পথ ছেড়ে বনে ঢুকেছিলাম, ভাবলে নাসিরুদ্দিন। এই মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশেই যদি এমন বিপদ লুকিয়ে থাকে, তা হলে না-জানি ধুলোকাদায় ভরা রাস্তায় কত নাজেহাল হতে হত!
.
২.
মোগ্লাগিন্নি একটা শব্দ পেয়ে ছুটে গেছে তার স্বামীর ঘরে।
কী হল? কীসের শব্দ?
আমার জোব্বাটা মাটিতে পড়ে গে, বললে মোল্লাসাহেব।
তাতেই এত শব্দ?
আমি ছিলাম জোব্বার ভেতর।
.
৩.
নাসিরুদ্দিন একদিন রাজসভায় হাজির হল মাথায় এক বিশাল বাহারের পাগড়ি নিয়ে। তার মতলব সে রাজাকে পাগড়িটা বিক্রি করবে।
তোমার ওই আশ্চর্য পাগড়িটা কত মূল্যে খরিদ করলে মোল্লাসাহেব? রাজা প্রশ্ন করলেন।
সহস্র স্বর্ণমুদ্রা, শাহেন শা!
এক উজির মোল্লার মতলব আঁচ করে রাজার কানে ফিসফিস করে বললে, মুগ্ধ না হলে কেউ ওই পাগড়ির জন্য অত দাম দিতে পারে না, জাঁহাপনা।
রাজা মোল্লাকে বললেন, অত দাম কেন? একটা পাগড়ির জন্য এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা যে অবিশ্বাস্য।
মূল্যের কারণ আর কিছুই না, জাঁহাপনা, বললে নাসিরুদ্দিন, আমি জানি দুনিয়ায় কেবল একজন বাদশাই আছেন যিনি এই পাগড়ি খরিদ করতে পারেন।
তোষামোদে খুশি হয়ে রাজা তৎক্ষণাৎ মোল্লাকে দুহাজার স্বর্ণমুদ্রা দেবার ব্যবস্থা করে নিজে পাগড়িটা কিনে নিলেন।
মোল্লা পরে সেই উজিরকে বললে, আপনি পাগড়ির মূল্য জানতে পারেন, কিন্তু আমি জানি রাজাদের দুর্বলতা কোথায়।
.
৪.
বোগদাদের খালিফের প্রাসাদে ভোজ হবে, তিন হাজার হোমরা-চোমরার নেমন্তন্ন হয়েছে। ঘটনাচক্রে নাসিরুদ্দিনও সেই দলে পড়ে গেছে।
খালিফের বাড়িতে ভোজ, চাট্টিখানি কথা নয়! অতিথি সৎকারে খালিফের জুড়ি দুনিয়ায় নেই। তেমনি তাঁর বাবুর্চিটিও একটি প্রবাদপুরুষ। তার রান্নার যেমনি স্বাদ, তেমনি গন্ধ, তেমনি চেহারা।
সব খাদ্যের শেষে বিরাট পাত্রে এল একেকটি আস্ত ময়ূর। দেখে মনে হবে ময়ূর বুঝি জ্যান্ত, যদিও আসলে সেগুলো রোস্ট করা। ডানা, ঠোঁট, পুচ্ছ সবই আছে, আর সবকিছুই তৈরি রঙবেরঙের উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য দিয়ে।
নিমন্ত্রিতেরা মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে আছে রন্ধনশিল্পের এই অপূর্ব নিদর্শনের দিকে, কেউই যেন আর খাবার কথা ভাবছে না।
নাসিরুদ্দিনের খিদে এখনও মেটেনি। সে কিছুক্ষণ ব্যাপার-স্যাপার দেখে আর থাকতে না পেরে বলে উঠল, এই বিচিত্র প্রাণীটি আমাদের ভক্ষণ করার আগে আমাদেরই এটিকে ভক্ষণ করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না কি?
.
৫.
নাসিরুদ্দিন একটি সরাইখানার তত্ত্বাবধায়কের কাজে বহাল হন্মেছে। একদিন সেখানে স্বয়ং সম্রাট সদলবলে এসে বললেন, তিনি ডিমভাজা খাবেন।
খাওয়া শেষ করে শাহেন শা নাসিরুদ্দিনকে বললেন, এবার শিকারে যাব। বলল কত দিতে হবে তোমাদের?
জাঁহাপনা, বললে নাসিরুদ্দিন, ডিমভাজার জন্য লাগবে সহস্র স্বর্ণমুদ্রা। সম্রাটের চোখ কপালে উঠল। ডিম কি এখানে এতই দুষ্প্রাপ্য? তিনি প্রশ্ন করলেন।
আজ্ঞে না জাঁহাপনা, বললে নাসিরুদ্দিন। ডিম দুষ্প্রাপ্য নয়। দুষ্প্রাপ্য সম্রাটের মতো খদ্দের।
সন্দে, আষাঢ় ১৩৮১
.
মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে সত্যজিৎ রায়ের লেখা ভূমিকা–
মোল্লা নাসিরুদ্দিনের নামে অনেক গল্প প্রায় হাজার হাজার বছর ধরে পৃথিবীর নানান দেশে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকের মতে এইসব গল্পের জন্ম তুরস্কদেশে, কারণ সেখানে এখনো প্রতি বছর মোল্লা নাসিরুদ্দিনের জন্মোৎসব পালন করা হয়।
মোল্লা নাসিরুদ্দিন যে ঠিক কেমন লোক ছিলেন সেটা তার গল্প পড়ে বোঝা মুশকিল। এক এক সময় তাকে মনে হয় বোকা, আবার এক এক সময় মনে হয় ভারী বিজ্ঞ। তোমাদের কী মনে হয় সেটা তোমরাই বুঝে নিও।
ইহুদির কবচ
১.
প্রাচ্যের পুরাতত্ত্ব সম্পর্কে আমার বিশিষ্ট বন্ধু ওয়র্ড মর্টিমারের জ্ঞান ছিল অসামান্য। সে এ বিষয়ে বিস্তর প্রবন্ধ লিখেছিল, মিশরের ভ্যালি অফ দ্য কিংস-এ খননকার্য তদারকের সময় একটানা দু বছর থিবিসের একটি সমাধিগৃহে বাস করেছিল, আর যে কাজটা করে সবচেয়ে বেশি সাড়া জাগিয়েছিল, সেটা হল ফাইলিতে হোরাসের মন্দিরের একটি ভিতরের ঘরে ক্লিওপ্যাট্রার মমি আবিষ্কার। মাত্র একত্রিশ বছর বয়সে যে লোক এত কিছু করতে পেরেছে, তার ভবিষ্যৎ যে উজ্জ্বল হতে বাধ্য, সেটা প্রায় সকলেই বিশ্বাস করত। তাই মর্টিমার যখন বেলমোর স্ট্রিট মিউজিয়মের তত্ত্বাবধায়কের কাজটা পেল, তখন কেউই বিশেষ অবাক হয়নি। এই পদ যিনি পাবেন, তিনি সেইসঙ্গে ওরিয়েন্টাল কলেজের অধ্যাপকের পদেও অধিষ্ঠিত হবেন, এবং তার ফলে তাঁর মাসিক রোজগার যা হবে, তাতে সচ্ছল জীবনযাত্রার সঙ্গে গবেষণার কাজও চালানো যায়।
শুধু একটা কারণেই ওয়র্ড মর্টিমার কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করছিল। সেটা হল, যে-তত্ত্বাবধায়কের স্থান সে দখল করেছিল, তাঁর অতুল খ্যাতি। প্রোফেসর অ্যাড্রিয়াসের পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ, এবং খ্যাতি সারা ইউরোপ জোড়া। দেশ-বিদেশ থেকে তরুণ ছাত্ররা আসত তাঁর বক্তৃতা শুনতে। তা ছাড়া মিউজিয়মের মহামূল্য সম্পদ সংরক্ষণের জন্য তিনি যে ব্যবস্থা করেছিলেন, সকলেই একবাক্যে তার প্রশংসা করত। ফলে পঞ্চান্ন বছর বয়সে তিনি হঠাৎ এমন একটি চাকরি ছেড়ে দেওয়াতে সকলেই বেশ অবাক হয়েছিল। ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাড্রিয়াস স্বভাবতই তাঁর মেয়েকে নিয়ে মিউজিয়ম-সংলগ্ন তাঁর বাসস্থান ত্যাগ করে চলে যান, আর তাঁর ঘরগুলি দখল করে আমার অকৃতদার বন্ধু ওয়র্ড মর্টিমার। চাকরিটা পাবার কয়েকদিনের মধ্যেই মর্টিমারকে চিঠি লিখে অভিনন্দন জানালেন প্রোফেসর অ্যাড্রিয়াস। যেদিন প্রথম এই দুজনের পরিচয় হয় পরস্পরের সঙ্গে, সেদিন আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম। অ্যাড্রিয়াস সেদিন তাঁর সংগ্রহশালার আশ্চর্য জিনিসগুলি আমাদের দেখালেন। প্রোফেসরের সুন্দরী মেয়ে এবং উইলসন নামে একটি যুবক (বোঝাই যাচ্ছিল। ইনি অধ্যাপক-দুহিতার পাণিপ্রার্থী) আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সংগ্রহশালায় সবসুদ্ধ পনেরোটি ঘর; তার মধ্যে ব্যাবিলন ও সিরিয়ার সভ্যতা সংক্রান্ত দুটি, আর সংগ্রহশালার ঠিক মাঝখানে অবস্থিত প্রাচীন মিশরীয় ও ইহুদি সভ্যতা সংক্রান্ত একটি ঘরই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। প্রোফেসর অ্যাড্রিয়াস এমনিতে চুপচাপ মানুষ, কিন্তু তাঁর সংগ্রহের প্রিয় জিনিসগুলি দেখাবার সময় তাঁর শ্মশুগুহীন শুকনো মুখখানা উৎসাহে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। পুরাতত্ত্বের এই মহামূল্য নিদর্শনগুলির উপর থেকে তাঁর হাত যেন আর সরতে চায় না। বেশ বোঝা যায় সেগুলি তাঁর গর্বের বস্তু, এবং সেগুলি অন্যের আওতায় চলে যাওয়াটা যেন তাঁর পক্ষে এক মর্মান্তিক ঘটনা।
তাঁর সংগ্রহশালার মমিগুলি, তাঁর প্রাচীন পুঁথির সম্ভার, তাঁর স্ক্যারাবের সংগ্রহ, ইহুদি সভ্যতার যাবতীয় নিদর্শন, আর টাইটাস কর্তৃক রোম শহরে আনা বিখ্যাত সপ্তপ্রদীপের অবিকল প্রতিরূপ (আসলটি টাইবার নদীগর্ভে নিমজ্জিত)–এ সবই একের পর এক আমাদের দেখালেন প্রোফেসর অ্যাড্রিয়াস। তারপর তিনি হলঘরের ঠিক মাঝখানে রাখা একটি শো-কেসের দিকে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গিয়ে গভীর সম্ভ্রমের সঙ্গে তার উপর ঝুঁকে পড়লেন।
আপনার মতো বিশেষজ্ঞের পক্ষে এ জিনিসটা হয়তো তেমন বিস্ময়কর কিছু নয়, মর্টিমারকে উদ্দেশ করে বললেন প্রোফেসর অ্যাড্রিয়াস, কিন্তু আপনার বন্ধু মিঃ জ্যাকসনের পক্ষে হওয়া উচিত।
এবার আমিও কাঁচের আবরণের উপর ঝুঁকে পড়ে দেখলাম, কেসের ভিতর রাখা রয়েছে হাতের তেলোর মতো বড় সূক্ষ্ম কারুকার্য করা একটি চতুষ্কোণ সোনার পাত, যার উপর তিন সারিতে চারটি-চারটি করে পাথর বসানো। পাতটির একদিকে দুই কোণে দুটি সোনার আংটা। সমান আয়তনের পাথরগুলো প্রত্যেকটি আলাদা জাতের এবং রঙের। রঙের বাক্সে পাশাপাশি খোপে খোপে যেমন বিভিন্ন রঙ সাজানো থাকে, এ যেন কতকটা সেইরকম। এও দেখলাম যে, প্রত্যেকটি পাথরের উপর একটি করে বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন খোদাই করা আছে।
মিঃ জ্যাকসন, আপনি কি উরিম ও থুমিমের কথা জানেন?
নামগুলো আমার চেনা, কিন্তু তাদের মানে জিজ্ঞেস করলে বলতে পারব না।
প্রোফেসর বললেন, ইহুদিদের প্রধান পুরোহিতের বুকে যে কবচটা ঝুলত, তাকেই বলা হত উরিম ও থুমিম। ইহুদিরা এই কবচের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করত, যেমন রোমানরা করত ক্যাপিটলে রাখা সিবিলাইন পুঁথিগুলির প্রতি। সাংকেতিক চিহ্ন-আঁকা বারোটি মহামূল্য রত্ন দেখতে পাচ্ছেন। উপরে বাঁ দিক থেকে শুরু করে পাথরগুলি হল কার্নেলিয়ান, পেরিডট, এমারেল্ড, রুবি, ল্যাপিস ল্যাজুলি, অনিক্স, অ্যাগেট, অ্যামেথিস্ট, টোপ্যাজ, বেরিল আর জ্যাসপার।
আমি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইলাম মণিমুক্তোখচিত মহামূল্য কবচটার দিকে। শেষে প্রশ্ন করলাম, এই কবচের সঙ্গে কি কোনও ঐতিহাসিক ঘটনা জড়িত আছে?
জিনিসটা যে অতি প্রাচীন এবং অতি মূল্যবান, তাতে কোনও সন্দেহ নেই, বললেন, প্রোফেসর। অ্যান্ড্রিয়াস। অকাট্য প্রমাণ না থাকলেও আমরা নানা কারণে বিশ্বাস করি যে, এটা সেই সলোমনের মন্দিরের আদি ও অকৃত্রিম উরিম ও থুমিম। এ জিনিস ইউরোপের কোনও মিউজিয়মে নেই। আমার তরুণ বন্ধু ক্যাপ্টেন উইলসন মণিমুক্তো সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। উনিই বলবেন এই পাথরগুলো কত খাঁটি।
তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ক্যাপ্টেন উইলসন দাঁড়িয়ে ছিলেন তাঁর ভাবী পত্নীর পাশেই। অল্প কথায় তিনি তাঁর মনের ভাব ব্যক্ত করলেন।
সত্যি কথা। আমি এর চেয়ে ভাল পাথর আর দেখিনি।
স্বর্ণকারের কাজও দেখার মতো, বললেন অ্যান্ড্রিয়াস। অতীতে স্বর্ণকারেরা–
প্রোফেসরের কথার উপর কথা চাপিয়ে উইলসন বললেন, ওর চেয়ে ভাল সোনার কাজের নিদর্শন দেখা যাবে এই মোমবাতিদানে। তাঁর দৃষ্টি এখন অন্য একটি টেবিলের দিকে। আমরা সকলেই শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট সোনার বাতিদানটার আশ্চর্য কারুকার্যের প্রশংসায় উইলসনের সঙ্গে গলা মেলালাম।
অ্যান্ড্রিয়াসের মতো বিশেষজ্ঞের চোখ দিয়ে এইসব আশ্চর্য জিনিস দেখা পরম সৌভাগ্যের কথা। সত্যি বলতে কি, সবকিছু দেখা শেষ হলে পর প্রোফেসর যখন আমার বন্ধুকে জানালেন যে, এখন থেকে এ সবই তার জিম্মায় চলে যাচ্ছে, তখন ভদ্রলোকের জন্য বেশ কষ্টই হচ্ছিল, আর সেইসঙ্গে আমার বন্ধুর সৌভাগ্যকে খানিকটা ঈষার চোখে না দেখে পারছিলাম না। এক সপ্তাহের মধ্যেই ওয়র্ড মর্টিমার বেলমোর স্ট্রিট মিউজিয়মের অধিকর্তা হিসাবে তার নতুন বাসস্থানে উঠে গেল।
এর দিন পনেরো পর মর্টিমার তার জনা-ছয়েক অকৃতদার বন্ধুদের সঙ্গে তার নতুন বাড়িতে একটা ভোজের আয়োজন করল। শেষে যখন সবাই যাবার জন্য উঠে পড়েছে, তখন মর্টিমার আমার কোটের আস্তিন ধরে একটা ছোট্ট টান দিয়ে বুঝিয়ে দিল যে, সে চায় আমি আর একটুক্ষণ থাকি।
তোমার বাড়ি তো এখান থেকে দশ-পা, বলল মর্টিমার (আমি তখন অ্যালব্যানিতে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি)–তুমি একটু থেকে যাও। চুরুট সহযোগে দুজনে নিরিবিলি কথা হবে। একটা ব্যাপারে তোমার পরামর্শের দরকার।
অগত্যা আমি একটি আরাম কেদারায় বসে মর্টিমারের একটি উৎকৃষ্ট ম্যাট্রোনাস চুরুট ধরালাম। সবাই চলে যাবার পরে সে পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে আমার সামনে বসল।
এই নামবিহীন চিঠিটা আজই সকালে এসেছে, বলল মর্টিমার। আমি পড়ে শোনাচ্ছি, তারপর তুমি বলো এ ব্যাপারে আমার কী কর্তব্য।
বেশ তো আমার সাধ্যমতো পরামর্শ দিতে আমি প্রস্তুত।
চিঠিটা হচ্ছে এই–মহাশয়, আপনার জিম্মায় যে সমস্ত মহামূল্য সম্পদ রয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে আপনাকে বিশেষ সাবধান হতে বলি। বর্তমান ব্যবস্থা অনুযায়ী একটিমাত্র পাহারাদারে কাজ হবে বলে আমি মনে করি না। আপনি এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে অপূরণীয় ক্ষতি হবার সম্ভাবনা আছে।
এই কি পুরো চিঠি?
হ্যাঁ।
অন্তত এটুকু বোঝা যাচ্ছে যে, তোমাদের ওখানে রাত্রে যে একটিমাত্র পাহারাদার থাকে, সে-খবরটা মুষ্টিমেয় যে কজন জানে, তাদেরই একজন লিখেছে এ চিঠি।
মর্টিমার এবার একটা রহস্যজনক হাসি হেসে চিঠিটা আমার হাতে দিল।
হস্তলিপি ব্যাপারটা নিয়ে তুমি কোনও চর্চা করেছ? প্রশ্নটা করে মর্টিমার আর-একটা চিঠি আমার সামনে রেখে বলল, এটার কনগ্রাচুলেটে সি-এর সঙ্গে ওটার কমিটেড-এর সি মিলিয়ে দেখো। ক্যাপিটাল আই-টাও লক্ষ করো, আর ফুলস্টপের জায়গায় ড্যাশ-চিহ্ন ব্যবহার করাটা। আমি বললাম, দুটো চিঠি নিঃসন্দেহে একই লোকের লেখা, যদিও প্রথমটায় হাতের লেখা গোপন করার একটা প্রয়াস লক্ষ করা যাচ্ছে।
দ্বিতীয় চিঠিটা হচ্ছে আমার এই নতুন চাকরিটা পাবার খবর পেয়ে প্রোফেসর অ্যান্ড্রিয়াসের অভিনন্দন পত্র।
আমি অবাক হয়ে চাইলাম মর্টিমারের দিকে, তারপর দ্বিতীয় চিঠিটা ওলটাতেই মার্টিন অ্যান্ড্রিয়াস সইটা চোখে পড়ল। যে তোক হাতের লেখা নিয়ে সামান্যতম চচাও করেছে, তার মনে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না যে, প্রোফেসর অ্যাড্রিয়াসই মিউজিয়মের সদ্য-ভারপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ককে চুরির ব্যাপারে সাবধান হতে বলে এই নামহীন চিঠিটা লিখেছেন। ঘটনাটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি।
কিন্তু ভদ্রলোক এমন চিঠি লিখবেন কেন? আমি প্রশ্ন করলাম।
ঠিক এই প্রশ্নই আমি করতে চাই তোমাকে। তাঁর মনে যদি এ ধরনের আশঙ্কা থেকেই থাকে, তা হলে তো তিনি নিজে এসে আমাকে বলতে পারতেন।
তুমি কি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে চাও?
সেখানেও তো গণ্ডগোল। উনি তো সোজাসুজি অস্বীকার করতে পারেন যে, চিঠিটা উনি লেখেননি।
যাই হোক–এ চিঠির উদ্দেশ্য যে সৎ, তাতে তো কোনও সন্দেহ নেই। উনি যে পরামর্শ দিয়েছেন, সেটা মানতে কোনও বাধা আছে কি? এখন যে ব্যবস্থা চালু আছে, সেটা কি সতর্কতার দিক দিয়ে যথেষ্ট?
আমার তো তাই বিশ্বাস। দর্শকদের জন্য মিউজিয়ম খোলা থাকে দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত। সেই সময়টা পাশাপাশি দুটো ঘরের জন্য একটি করে গার্ড মোতায়েন থাকে। দুটো ঘরের মাঝখানে যে দরজা–সেখানে দাঁড়ায় গার্ড, ফলে একসঙ্গে দুটো ঘরেই সে চোখ রাখতে পারে।
কিন্তু রাত্রে?
পাঁচটার পর লোহার গেটগুলো সব বন্ধ করে দেওয়া হয়। সে গেট খোলার সাধ্যি কোনও চোরের নেই। যে পাহারা দেয়, সে অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক। সে তিন ঘণ্টা অন্তর অন্তর তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সারা মিউজিয়মটা টহল দেয়। প্রত্যেকটি ঘরে একটি করে বিজলিবাতি সারারাত জ্বলে।
তা হলে একমাত্র উপায় হচ্ছে গার্ডগুলিকে রাত্রেও রেখে দেওয়া।
সেটা খরচে পোষাবে না।
অন্তত পুলিশে খবর দিয়ে বললো যে, বেলমোর স্ট্রিটে তারা যেন একটি বিশেষ কনস্টেবলের ব্যবস্থা করে। এই চিঠি যিনি লিখেছেন তিনি যদি তাঁর পরিচয় গোপন করতে চান, তা হলে কিছু বলার নেই। কেন তিনি এটা চাইছেন, সেটা আশা করি এর পর কী ঘটে তার থেকেই বোঝা যাবে।
এর পর অবিশ্যি এ বিষয়ে আলোচনা করার আর কিছু রইল না। আমি বাড়ি ফেরার পর সারারাত মাথা ঘামিয়েও প্রোফেসর অ্যাড্রিয়াসের চিঠির পিছনে আসল উদ্দেশ্যটা কী, সেটা বুঝতে পারলাম না। এ চিঠি যে তাঁরই লেখা সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। মিউজিয়মে যে চোরের উপদ্রব হতে পারে, সেটা তিনি আঁচ করেছিলেন; সেই কারণেই কি তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিলেন? কিন্তু তাই যদি হয়, তা হলে সরাসরি মর্টিমারকে সতর্ক করলেন না কেন? আমি অনেক ভেবেও রহস্যের কিনারা করতে না পেরে শেষরাত্রে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম, ফলে আমার উঠতেও দেরি হয়ে গেল।
ঘুমটা ভাঙলও আশ্চর্যভাবে। নটা নাগাদ মর্টিমার হন্তদন্ত হয়ে এসে আমার দরজায় টোকা মেরে ঘরে ঢুকল। তার চাহনিতে গভীর উদ্বেগ। এমনিতে পোশাক-আশাকের ব্যাপারে মর্টিমার খুব পরিপাটি। কিন্তু আজ দেখি তার শার্টের কলার প্রায় খুলে এসেছে, গলার টাই আর মাথার টুপিরও প্রায় সেই দশা। তার সন্ত্রস্ত দৃষ্টি থেকে মোটামুটি বোঝা যায় কী ঘটেছে।
আমি তৎক্ষণাৎ বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে বললাম, মিউজিয়মে চোর এসেছিল বুঝি?
ঠিকই ধরেছ। সেই পাথরগুলো–উরিম আর থুমিমের সেই অমূল্য পাথরগুলো! দৌড়ে আসার ফলে মর্টিমার হাঁফাচ্ছে। আমি চললাম থানায়। তুমি যত শিগগির পায়রা চলে এসো জ্যাকসন–গুড বাই!
উদভ্রান্তভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মর্টিমার, আর পরক্ষণেই শুনলাম তার দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়ে নামার শব্দ।
আমি ওর কথামতো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মিউজিয়মে পৌঁছে দেখি, মর্টিমার এর মধ্যেই একটি ইনস্পেক্টর ও আর একটি ভদ্রলোককে নিয়ে এসেছে। ভদ্রলোকটি হলেন মিঃ পার্ভিস–বিখ্যাত হীরক ব্যবসায়ী মবসন অ্যাণ্ড কোং-এর একজন অংশীদার। নামকরা জহুরি হিসাবে ইনি পাথর চুরির ব্যাপারে পুলিশকে সাহায্য করতে সদা প্রস্তুত। ইহুদির কবচটা যে শো-কেসের মধ্যে ছিল, সেটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনজন। কবচটা এখন বাইরে বার করে কাঁচের আচ্ছাদনটার উপর রাখা হয়েছে, আর তিনজনে গভীর মনোযোগের সঙ্গে সেটাকে পরীক্ষা করছে।
কবচটার উপর যে মানুষের হাত পড়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই, বলল মর্টিমার। আজ সকালে এটার দিকে চোখ যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার সন্দেহ হয়। কাল রাত্রেও আমি এটা দেখেছি, তখন ঠিকই ছিল। অর্থাৎ কুকীর্তিটা হয়েছে মাঝরাত্রে।
মর্টিমার ঠিকই বলেছে; কবচটা নিয়ে কেউ ঘাঁটাঘাঁটি করেছে। প্রথম সারির চারটে পাথরকে ঘিরে সোনার উপর ক্ষতচিহ্ন। পাথরগুলো তাদের জায়গাতেই রয়েছে; ক্ষতি যা হয়েছে, সেটা সোনার সূক্ষ্ম কারুকার্যে–যার সৌন্দর্যের তারিফ আমরা এই কদিন আগেই করেছি।
ইনস্পেক্টর সাহেব বললেন, দেখে মনে হচ্ছে, কেউ যেন পাথরগুলোকে উপড়ে ফেলার চেষ্টা করেছিল।
মর্টিমার বলল, আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, শুধু চেষ্টাই করেনি, কৃতকার্য হয়েছিল। আমার ধারণা, প্রথম সারির চারটে পাথরই নকল, যদিও চোখে দেখে ধরার উপায় নেই।
জহুরি মশাইয়েরও মনে হয়তো একই সন্দেহের উদয় হয়েছিল, কারণ তিনি এখন আতশ কাঁচের সাহায্যে অতি মনোযোগের সঙ্গে পাথরগুলো যাচাই করছেন। কাঁচের সাহায্য ছাড়াও নানাভাবে সেগুলোকে পরীক্ষা করে অবশেষে মর্টিমারের দিকে চেয়ে একগাল হেসে ভদ্রলোক বললেন, আপনার কপাল ভাল। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, প্রথম সারির চারটে পাথরই খাঁটি। এত নিখুঁত পাথর সচরাচর দেখা যায় না।
আমার বন্ধুর মুখ থেকে ফ্যাকাশে ভাবটা চলে গেল। সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল, যাক, বাবা! কিন্তু তা হলে চোরের উদ্দেশ্যটা ছিল কী?
হয়তো পাথরগুলো নেওয়ার মতলবেই এসেছিল, কিন্তু সেকাজে বাধা পড়ে।
কিন্তু নেওয়াই যদি উদ্দেশ্য হবে, তা হলে তো একটা একটা করে খুলে নেওয়া উচিত। এখানে দেখছি চারটে পাথরকেই আলগা করার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু একটাকেও নেওয়া হয়নি।
ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক, বললেন ইনস্পেক্টর সাহেব। ঠিক এরকম ঘটনা আর একটাও মনে পড়ছে না। চলুন, একবার পাহারাদারের সঙ্গে কথা বলা যাক।
প্রহরীকে ডেকে আনানো হল। মজবুত, মিলিটারি গড়ন, চেহারায় সততার ছাপ, গত রাত্রের ঘটনায় সে তার মনিবের মতোই বিচলিত।
না স্যার, আমি কোনও আওয়াজ পাইনি। ইনস্পেক্টরের প্রশ্নের উত্তরে সে বলল। আমি যেমন রোজ করি, তেমনই কাল রাত্রেও তিনবার টহল দিয়েছি, কিন্তু সন্দেহজনক কিছু দেখিনি। আমি গত দশ বছর এই কাজ করছি; এমন ঘটনা আমার আমলে এর আগে কখনও ঘটেনি।
কোনও জানলা দিয়ে চোর ঢুকতে পারে কি?
অসম্ভব স্যার!
তোমার ঘরের সামনে দিয়ে কেউ গিয়ে থাকতে পারে?
না স্যার। টহল দেবার সময়টুকু ছাড়া আমি সারাক্ষণ আমার ঘরের বাইরে বসে থাকি।
মিউজিয়মে ঢোকার আর কী পথ আছে?
মিঃ মর্টিমারের কোয়ার্টাসের একটা প্রাইভেট দরজা দিয়ে মিউজিয়মে ঢোকা যায়।
সে দরজা রাত্রে চাবি দিয়ে বন্ধ থাকে, বলল মর্টিমার। আর সেটায় পৌঁছতে হলে আগে মিউজিয়মের সদর দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকতে হয়।
আপনার চাকরবাকর?
তাদের থাকবার জায়গা একেবারে আলাদা।
ব্যাপারটা বেশ ঘোলাটে, তাতে সন্দেহ নেই–বললেন ইনস্পেক্টর। অবিশ্যি মিঃ পার্ভিসের মতে আপনার কোনও ক্ষতি হয়নি।
আমি শপথ করে বলতে পারি, প্রথম সারির চারটে পাথর একেবারে খাঁটি, আবার বললেন মিঃ পার্ভিস।
তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে যে, চোরের একমাত্র উদ্দেশ্য হল কবচটাকে জখম করা, বললেন ইনস্পেক্টর সাহেব, তা সত্ত্বেও একবার দালানটা ঘুরে দেখায় কোনও ক্ষতি আছে বলে মনে করি না। হয়তো তার ফলে কে এই রহস্যময় চোর, তার কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে।
সারা সকাল পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধানেও কোনও ফল হল না। মিউজিয়মে ঢোকার যে আরও দুটো সম্ভাব্য পথ আছে, সেটা ইনস্পেক্টর সাহেব আমাদের দেখালেন। একটা হল মাটির নীচে সেলারের মাথায় একটা চোরা দরজা, আর দ্বিতীয় হল মাথার উপরে একটি অকেজো জিনিসপত্র রাখার ঘর বা লাম্বার রুমের স্কাইলাইট। এই ঘরের একটা বিশেষ স্কাইলাইট দিয়ে নীচে মিশরীয় ও ইহুদি জিনিসের ঘরটা পরিষ্কার দেখা যায়। তবে এই দুটো প্রবেশপথের যে-কোনও একটা ব্যবহার করতে গেলেই চোরকে আগে ঢুকতে হবে দালানের মধ্যে। কিন্তু সে পথ যেহেতু বন্ধ, আর সেলার এবং লাম্বার রুম দুটোতেই যে পরিমাণ ধুলো জমে রয়েছে, এই দুটো প্রবেশপথের কথাই ওঠে না। শেষ পর্যন্ত কে, কখন, কেন কুকীর্তিটা করেছে সে রহস্যের কোনও কিনারা হল না।
আর একটিমাত্র পথ মর্টিমারের সামনে খোলা আছে, এবং শেষ পর্যন্ত সে সেটাই নিল। পুলিশদের তাদের কাজ চালিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে সে আমাকে অনুরোধ করল সে দিনই বিকেলে তার সঙ্গে প্রোফেসর অ্যাড্রিয়াসের ওখানে যেতে। যাবার সময় সে সঙ্গে চিঠি দুটো নিয়ে নিল, উদ্দেশ্য, প্রোফেসরকে সরাসরি জিজ্ঞেস করা তিনি কেন নামবিহীন চিঠিটা লিখেছিলেন এবং কী করে তিনি অনুমান করলেন যে, মিউজিয়ামে এইরকম একটা দুর্ঘটনা ঘটবে। আপার নরউডে একটা ছোট বাড়িতে প্রোফেসর থাকেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে বাড়ির এক পরিচারিকার কাছ থেকে জানলাম যে, প্রোফেসর শহরে নেই। এই খবরে আমরা দুজনেই খুব হতাশ হয়েছি দেখে পরিচারিকা বললেন, আমরা যদি বৈঠকখানায় গিয়ে বসি, তা হলে তিনি প্রোফেসরের মেয়ের সঙ্গে আমাদের দেখা করিয়ে দেবেন।
আগেই বলেছি যে, অ্যাড্রিয়াসের কন্যাটি সুন্দরী। দীর্ঘ ছিমছাম তার গড়ন, মাথার চুল সোনালি, গায়ের রঙ ও মসৃণতা গোলাপের পাপড়ির কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু সে যখন ঘরে ঢুকল, তখন এই দু-সপ্তাহে তার কত পরিবর্তন হয়েছে দেখে আমি প্রায় চমকে উঠলাম। তার চাহনিতে গভীর সংশয়ের ছাপ।
বাবা গেছেন স্কটল্যান্ডে, বললেন মহিলা। উনি বড় ক্লান্ত বোধ করছিলেন, তার উপর দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। উনি কালই চলে গেছেন।
আপনাকেও যেন ক্লান্ত দেখছি, মিস অ্যাড্রিয়াস, বলল আমার বন্ধু।
সেটা হয়েছে বাবার সম্বন্ধে চিন্তা করেই।
ওঁর স্কটল্যান্ডের ঠিকানা আপনার কাছে আছে কি?
হ্যাঁ। উনি রয়েছেন ওঁর ভাই রেভারেন্ড ডেভিড অ্যাড্রিয়াসের বাড়িতে। ঠিকানা, এক নম্বর আরাম ভিলা, আরড্রোস্যান।
মর্টিমার ঠিকানাটা লিখে নেবার পর আমরা আমাদের আসার উদ্দেশ্যটা না জানিয়েই বিদায় নিলাম। সন্ধ্যায় আমরা দুজনে ঠিক সকালের মতোই আবার বেলমোর স্ট্রিটে মিলিত হলাম। প্রোফেসরের চিঠিই আমাদের একমাত্র কু। মর্টিমার স্থির করেছিল পরদিনই আরড্রোস্যানে গিয়ে প্রোফেসরকে চিঠিটা দেখিয়ে একটা হেস্তনেস্ত করবে, এমন সময় একটা ঘটনার ফলে তার পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে গেল।
পরদিন ভোরে আমার দরজায় টোকার শব্দে ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে দেখি, একটি লোকের হাতে মর্টিমারের একটা চিঠি। সে লিখছে, অবিলম্বে চলে এসো। রহস্য আরও জটিল হয়ে উঠেছে।
আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই মিউজিয়মে পৌঁছে দেখলাম মর্টিমার মাঝের ঘরটায় উদ্বিগ্নভাবে পায়চারি করছে, আর ঘরের একপাশে পল্টনের মতো দাঁড়িয়ে আছেন প্রহরীমশাই।
ওঃ জ্যাকসন! তোমায় আমার বিশেষ প্রয়োজন। এ রহস্যের কুলকিনারা করা আমার কম্ম নয়।
আবার কী হল?
মর্টিমার কাঁচের শো-কেসটার দিকে হাত দেখিয়ে বলল, যাও, নিজেই দেখো গিয়ে।
আমি যা দেখলাম, তাতে আপনা থেকেই আমার মুখ দিয়ে একটা বিস্ময়সূচক শব্দ বেরিয়ে পড়ল। এবার মাঝের সারির পাথরগুলোর অবস্থাও হুবহু উপরের সারির মতো। বারোটার মধ্যে আটটা পাথরের উপর দুবৃত্তের হাত পড়েছে। শেষের সারির পাথরগুলো যেমন ছিল তেমনই আছে।
পাথরগুলো কি বদলানো হয়েছে? আমি প্রশ্ন করলাম।
না। মাঝের চারটের মধ্যে এমারেন্ডের রঙে সামান্য একটু বৈষম্য ছিল। এখনও সেটা। রয়েছে। কাজেই ধরে নেওয়া যায় যে, উপরের সারির মতো এগুলোও বদলানো হয়নি। আচ্ছা সিম্পসন, তুমি তো বলছ সন্দেহজনক কোনও শব্দ পাওনি।
না স্যার, প্রহরী জবাব দিল, কিন্তু সকাল হলে পর আমি এই ঘরে এসে কবচটা দেখেই বুঝলাম যে, ওটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করা হয়েছে। আমি তৎক্ষণাৎ আপনাকে খবর দিই। কিন্তু আমি যতক্ষণ পাহারা দিয়েছি ততক্ষণ কাউকে দেখিনি, কোনও শব্দও পাইনি।
মর্টিমার আমার দিকে ফিরে বলল, এসো আমার সঙ্গে, একটু ব্রেকফাস্ট করা যাক। তার ঘরে পৌঁছতেই সে ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করল, এসব কী ঘটছে বলো তো জ্যাকসন?
সত্যি বলতে কি, এমন অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা আমার অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বাইরে। আমি বললাম, আমার মতে এ কোনও উন্মাদের কীর্তি।
এর মধ্যে কোনও অর্থ খুঁজে পাচ্ছ না তুমি?
আমি একটু ভেবে বললাম, এই প্রাচীন কবচটা ইহুদিদের কাছে একটি অতি পবিত্র জিনিস। ধরো, যদি ইহুদি-বিরোধী কোনও দলের কেউ কবচটাকে নষ্ট
না, না, না! চেঁচিয়ে বলে উঠল মর্টিমার। ওটা কোনও কথাই হল না। এমন লোক হয়তো আছে যে কবচটাকে নষ্ট করতে চাইতে পারে, কিন্তু পাথরের চারধারে কুরে কুরে সেগুলোকে আলগা করার চেষ্টা করবে কেন? এর কারণ খুঁজতে হবে অন্য কোথাও। এখন বলো তো, টহলদার সিম্পসন সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা।
ওকে সন্দেহ করার কোনও কারণ আছে কি?
কারণ একমাত্র এই যে, রাত্রে এক সিম্পসন ছাড়া কেউ এ তল্লাটে থাকে না।
কিন্তু এমন অর্থহীন ধ্বংসের কাজ সে করবে কেন? কোনও জিনিস তো চুরি যায়নি।
ধরো যদি তার মাথা খারাপ হয়ে থাকে।
উঁহু। সিম্পসনের মাথায় কোনও গণ্ডগোল নেই, এটা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি।
তুমি নিজে অন্য কাউকে সন্দেহ করো?
তুমিই তো রয়েছ! আমি হালকা হেসে বললাম। ঘুমের মধ্যে হাঁটাহাঁটি করার ব্যারাম-ট্যারাম আছে নাকি তোমার?
মোটেই না।
তা হলে এ রহস্য সমাধানের কাজে আমি ইস্তফা দিলাম।
কিন্তু আমি দিচ্ছি না। একটা পন্থা আছে, যার সাহায্যে আমরা এর কিনারা করতে পারব। প্রোফেসর অ্যাড্রিয়াসের সঙ্গে দেখা করে?
না। স্কটল্যান্ড যাবার দরকার নেই। কী করব সেটা বলছি তোমাকে। ওপরের লাম্বার রুমের একটা স্কাইলাইট দিয়ে মাঝের হলঘরটা দেখা যায়, সেটা তো দেখলে। আমরা হলঘরে বাতি জ্বালিয়ে রেখে ওপরের স্কাইলাইটে চোখ লাগিয়ে বসে থাকব। তুমি আর আমি। দুজনে একজোটে রহস্যের সমাধান করব। যদি এই রহস্যময় ব্যক্তিটি এক-একদিনে চারটে করে পাথরের উপর কাজ করে, তা হলে সে নিশ্চয়ই আজ রাত্রে আবার এসে শেষ সারির চারটে পাথর নিয়ে পড়বে।
উত্তম প্রস্তাব।
আমরা ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন রাখব। পুলিশ বা সিম্পসন, কাউকেই কিছু বলব না। রাজি?
অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে রাজি।
.
২.
রাত দশটা নাগাদ আমি মর্টিমারের বাড়িতে গিয়ে হাজির হলাম। তাকে দেখেই বুঝলাম, সে একটা চাপা উত্তেজনার মধ্যে রয়েছে। হাতে সময় আছে, তাই আমরা দুজনে মর্টিমারের ঘরে বসে ঘণ্টাখানেক ধরে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করলাম। অবশেষে একটা সময় এল, যখন রাস্তায় গাড়িঘোড়া পথচারী ইত্যাদির শব্দ কমে গিয়ে পাড়াটা নিস্তব্ধ হয়ে এল। প্রায় বারোটার সময় মর্টিমার আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল অকেজো জিনিসপত্র রাখার ঘরটাতে।
ইতিমধ্যে দিনের বেলায় একবার ঘরটাতে এসে মর্টিমার আমাদের বসার সুবিধার জন্য মেঝেতে চট বিছিয়ে রেখেছে। স্কাইলাইটের শার্সিগুলো স্বচ্ছ কাঁচের তৈরি হলেও তার উপর ধুলো পড়ে এমন। দশা হয়েছে যে, আমরা নীচের ঘরটা মোটামুটি দেখতে পেলেও, নীচ থেকে কেউ আমাদের দেখতে পাবে না। কাঁচের উপর দুটো ছোট্ট অংশ থেকে ধুলো মুছে ফেলে সেইখানে আমাদের চোখ। লাগানোর ব্যবস্থা করলাম। বিজলি বাতির উজ্জ্বল আলোতে হলঘরের সব কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, এমনকী শো-কেসের ভিতরের জিনিসগুলো পর্যন্ত। ঘরে একপাশে দরজার ধারে দাঁড় করানো মিশরীয় মমি-কেস থেকে শুরু করে কাঁচের শো-কেসে রাখা ইহুদির কবচের প্রত্যেকটি ঝলমলে পাথর–সবকিছুই আমরা দেখছি সমান আগ্রহের সঙ্গে। ঘরে মণিমুক্তোর ছড়াছড়ি। কিন্তু কবচের উরিম ও ঘুমিমের বারোটা পাথরের জেল্লা অন্য সব কিছুকে ম্লান করে দিয়েছে। সিকারার সমাধি মন্দিরের ছবি, কাণাকের প্রাচীরচিত্র, মেমফিসের ভাস্কর্য, থিবিসের প্রস্তরলিপি–সবই তন্ময় হয়ে দেখার জিনিস; কিন্তু তা সত্ত্বেও চোখ বারবার চলে যায় কাঁচের নীচে কবচটার দিকে, আর মন উদগ্রীব হয়ে ওঠে ওর রহস্য ভেদ করার জন্য। আমি এই রহস্যের কথাই ভাবছি, এমন সময় আমার বন্ধুটি হঠাৎ নিশ্বাস টেনে আমার কোটের আস্তিনটা সজোরে খামচে ধরল। পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলাম এর কারণ।
হলঘরের দরজার পাশে রাখা মমি-কেসটার কথা আগেই বলেছি। অবাক বিস্ময়ে দেখলাম, দাঁড় করানো মমি-কেসটার ডালাটা খুলতে শুরু করেছে। খোলার ফলে যে সরু কালো ফাঁকটার সৃষ্টি হয়েছে, সেটা অতি ধীরে ধীরে চওড়া হচ্ছে। এই ভোলার ব্যাপারটা এত সন্তর্পণে ঘটছে যে, ভাল করে না দেখলে চোখে ধরাই পড়ে না। একটু পরেই দেখলাম যে, ফাঁক দিয়ে একটা শীর্ণ হাত বেরিয়ে এসে নকশাদার ডালাটাকে ধরে সেটা আরও সামনে এগিয়ে দিল। তারপর বেরিয়ে এল অন্য হাতটা, আর তারপরেই একটা মুখ। এ-মুখ আমাদের দুজনেরই খুব চেনা। ইনি হলেন স্বয়ং প্রোফেসর অ্যাড্রিয়াস। এবার তাঁর পুরো শরীরটা শবাধার থেকে বেরিয়ে এল, শেয়াল যেমন বেরিয়ে আসে তার গর্ত থেকে। ভদ্রলোকের দৃষ্টি ঘুরছে এদিক-ওদিক, পা-দুটো একবার সামনে এগোচ্ছে, পরমুহূর্তেই থামছে, আবার দৃষ্টি ঘুরছে এদিক-ওদিক, আবার এগোচ্ছে পা। একবার রাস্তা থেকে আসা একটা অস্ফুট শব্দে তিনি থেমে গেলেন, কানখাড়া করে শুনতে লাগলেন, ভাবটা এই, যেন দরকার হলে তৎক্ষণাৎ আবার ফিরে যাবেন তাঁর লুকোনোর জায়গায়। কিন্তু সেটার প্রয়োজন। হল না। প্রোফেসর গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গিয়ে শো-কেসটার সামনে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে একটা চাবির গোছ বার করলেন। তারই একটা চাবি দিয়ে খোলা হল শো-কেসের ঢাকনা, বাইরে বেরিয়ে এল ইহুদির কবচ, আর সেটাকে ঢাকনার উপর রেখে একটা ছোট ধাতব যন্ত্র দিয়ে তার উপর কাজ শুরু করলেন প্রোফেসর। আমাদের একেবারে সরাসরি নীচে দাঁড়ানোর ফলে তাঁর ঝুঁকে-পড়া পিঠটা কবচটাকে ঢেকে দিয়েছে, কিন্তু তাঁর হাত যেভাবে চলছিল তাতে বুঝতেই পারছিলাম, যে-নষ্টামির পরিচয় আমরা পেয়েছি, সেই একই কাজে তিনি মগ্ন!
আমার বন্ধুর দ্রুত নিশ্বাসের আর আমার হাতের উপর তার হাতের চাপ থেকেই বুঝতে পারছি। প্রোফেসরের এই কুকীর্তিতে তার মনে কী প্রতিক্রিয়া হচ্ছে। অপকর্মের জন্য যে ইনিই দায়ী, সেটা। যে এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এই সেদিনই ইনি আমাদের কাছে ওই কবচের গুণগান করেছেন, আর আজ ইনিই সেই আশ্চর্য বস্তুটির সর্বনাশ করে চলেছেন! রাতদুপুরে এই কুকীর্তি যে কী অমানুষিক ভণ্ডামির পরিচয় বহন করে এবং তাঁর উত্তরাধিকারীর প্রতি কী পরিমাণ আক্রোশ যে এতে প্রকাশ পাচ্ছে, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। কাজটা ভাবতেও যেমন, দেখতেও ঠিক তেমনই পীড়াদায়ক। আমি নিজে এ ব্যাপারে মোটেই বিশেষজ্ঞ নই, কিন্তু তাও এই আশ্চর্য কবচের এহেন দুর্গতি আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠছিল। আমার সঙ্গীটি আমার হাতে একটা টান দিয়ে নিঃশব্দে ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে গেল। আমি তাকে অনুসরণ করলাম। নিজের ঘরে ফিরে আসার পর মর্টিমার মুখ খুলল।
লোকটা কতবড় শয়তান! এ জিনিস কি স্বপ্নেও ভাবা যায়?
ব্যাপারটা সত্যিই অবিশ্বাস্য।
হয় শয়তান, না হয় পাগল। এই দুটোর একটা হতেই হবে। আসল ব্যাপারটা শিগগিরই জানা যাবে। এসো আমার সঙ্গে; এখনই একটা এপার ওপার করা দরকার।
একটা প্যাসেজের শেষ প্রান্তে একটা দরজা দিয়ে সোজা মিউজিয়মে ঢোকা যায়। এটা একমাত্র তত্ত্বাবধায়কের ব্যবহারের জন্যই তৈরি। মর্টিমারের দেখাদেখি আমিও আগে পায়ের জুতো-জোড়া খুলে ফেললাম। তারপর নিঃশব্দে চাবি দিয়ে দরজাটা খুলে মিউজিয়মে ঢুকে ঘরের পর ঘর পেরিয়ে অবশেষে আসল ঘরে পৌঁছলাম। ভদ্রলোক এখনও তাঁর দুষ্কর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন। আমরা নিঃশব্দে তাঁর দিকে অগ্রসর হলাম। কিন্তু তাঁর কাছে পৌঁছনোর আগেই তিনি আমাদের উপস্থিতি টের পেয়ে চমকে ঘুরে একটা চাপা চিৎকার দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।
সিম্পসন! সিম্পসন। মর্টিমার তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অনেকগুলি দরজা পেরিয়ে শেষ দরজার মুখে বৃদ্ধ প্রহরী মশাইকে আবির্ভূত হতে দেখা গেল। প্রোফেসর অ্যাড্রিয়াসও একই সঙ্গে তাকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। পরমুহূর্তেই তাঁর পিঠে দু দিক থেকে আমাদের দুজনের হাত পড়ল।
ঠিক আছে, ঠিক আছে, হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন ভদ্রলোক! আমি যাচ্ছি আপনাদের সঙ্গে। আপনার ঘরেই চলুন মিঃ মর্টিমার। জবাবদিহির ব্যাপারটা ওখানেই সারা যাবে।
মর্টিমার ক্রোধে এত অধীর যে, তার মুখ দিয়ে কথাই বেরোল না। প্রোফেসরকে মাঝখানে রেখে আমরা তিনজন প্রথমে হলঘরে ফিরে এলাম, সিম্পসন আমাদের পিছনে। শো-কেসের উপর ঝুঁকে পড়ে মর্টিমার কাচটা পরীক্ষা করে দেখল। নীচের সারির প্রথম পাথরটা এর মধ্যেই খানিকটা আলগা হয়ে এসেছে। কবচটা হাতে নিয়ে মর্টিমার প্রোফেসরের দিকে ফিরল–তার দৃষ্টি যেন অগ্নিবর্ষণ করছে।
কী করে পারলেন আপনি, কী করে পারলেন।
কাজটা অত্যন্ত ঘৃণ্য আমি জানি, বললেন প্রোফেসর অ্যাড্রিয়াস। আপনার মনের ভাব আমি বুঝতে পারছি। আমি অনুরোধ করছি, আপনার ঘরে নিয়ে চলুন আমাকে।
কিন্তু এটাকে তো এভাবে ফেলে রাখা যায় না, বলল মর্টিমার। তারপর গভীর দরদের সঙ্গে সে কবচটাকে হাতে তুলে নিল। আমরা রওনা দিলাম। প্রোফেসরের পাশে আমি হাঁটছি, যেন পুলিশ চলেছে হাতেনাতে ধরা-পড়া চোরের পাশে। আমরা সোজা মর্টিমারের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। হতভম্ব সিম্পসন বাইরে রয়ে গেল তার নিজের বুদ্ধি দিয়ে ঘটনাটা অনুধাবন করবার জন্য; প্রোফেসর একটা সোফায় বসলেন। তাঁর শোচনীয় অবস্থা দেখে রাগের পরিবর্তে আমরা দুজনেই তাঁর সম্বন্ধে সংশয়ান্বিত বোধ করছিলাম। ব্র্যান্ডি খাবার পর তিনি খানিকটা প্রকৃতিস্থ হলেন।
এখন অনেকটা সুস্থ বোধ করছি, বললেন ভদ্রলোক। গত কদিনের ধকল আমাকে প্রায় শেষ করে দিয়েছে। আমি আর পেরে উঠছিলাম না। আমার পক্ষে এ এক চরম বিভীষিকা। একদিন যে-মিউজিয়ম আমারই জিম্মায় ছিল, সেই মিউজিয়মের ঘরেই আমাকে ধরা দিতে হল চোরের মতো! অথচ আপনাকেই বা দোষ দেব কী করে? আপনি আপনার কর্তব্য পালন করেছেন। আমি শুধু এটাই চেয়েছিলাম যে, কেউ টের পাবার আগে আমি যেন আমার কাজটা শেষ করতে পারি। সেটা আজ রাত্রেই হয়ে যেত, কিন্তু…।
আপনি ভিতরে ঢুকলেন কী করে? প্রশ্ন করল মর্টিমার।
আপনি যে দরজা ব্যবহার করেন, সেই দরজা দিয়ে, বললেন প্রোফেসর অ্যাড্রিয়াস। কাজটা অত্যন্ত গর্হিত, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ সৎ। সেখানে কোনও দোষ ধরতে পারবে না কেউ। আসল ঘটনাটা জানলে আপনিও আমাকে আর গাল দেবেন না। আপনার বাসস্থানের দরজার একটা চাবি আর মিউজিয়মে ঢোকার একটা চাবি আমার কাছে ছিল। চাকরি ছাড়ার সময় সেগুলি ফেরত দিইনি। মিউজিয়ম থেকে দর্শকের দল বাইরে বেরোনো মাত্র আমি হলঘরে ঢুকে মমি-কেসটার ভিতর লুকিয়ে পড়তাম। তার পর নিরাপদ বুঝে বেরিয়ে এসে যা করার তা করতাম। যতবার সিম্পসনের পায়ের শব্দ পেতাম, তত বারই আমাকে মমি-কেসের ভিতর আশ্রয় নিতে হত। তারপর কাজ শেষ হলে, যেভাবে ঢুকেছি সেই পথেই বেরিয়ে আসতাম।
তার মানে আপনি একটা মস্ত ঝুঁকি নিয়েছিলেন?
নিতেই হয়েছিল।
কিন্তু কেন? কোন উদ্দেশ্যে আপনাকে এরকম একটা জঘন্য কাজ করতে হল? পাশেই। টেবিলের উপর রাখা কবচটার দিকে হাত দেখিয়ে বলল মর্টিমার।
এ ছাড়া কোনও রাস্তা ছিল না। অনেক ভেবেও আর কোনও উপায় খুঁজে পাইনি। এ না করলে লোকমুখে আমার বদনাম ছড়িয়ে পড়ত আর সেইসঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনেও আমাকে গভীর শোক ভোগ করতে হত। আমি যা করেছি তা মঙ্গলের জন্যই, যদিও আপনার পক্ষে এটা বিশ্বাস করা কঠিন। আমি চাই আমার কথা সত্য প্রমাণ করার সুযোগ আপনি দেবেন।
আপনার কী বলার আছে শোনার পর আমি আমার কর্তব্য স্থির করব, দৃঢ়স্বরে বলল মর্টিমার।
আমি কিছুই গোপন রাখব না, সব কথা অকপটে আপনাকে বলব। তারপর আপনি কী করেন, সেটা আপনার মর্জি।
আসল ব্যাপারটা তো আর আমাদের জানতে বাকি নেই।
আসল ব্যাপার আপনি কিছুই জানেন না। প্রথমে কয়েক সপ্তাহ আগের একটা ঘটনায় ফিরে যেতে দিন, তারপর আমি সব বুঝিয়ে বলব। এটুকু বিশ্বাস করুন যে, আমি যা বলছি তার মধ্যে একবর্ণ মিথ্যে নেই।
যে ব্যক্তি ক্যাপ্টেন উইলসন বলে নিজের পরিচয় দেন, তার সঙ্গে আপনাদের আলাপ হয়েছে। আমি এইভাবে বলছি, কারণ আমি এখন জানতে পেরেছি যে, এটা তার আসল পরিচয় নয়। ওর সঙ্গে আমার কী করে আলাপ হল, কী করে সে আমার বিশ্বাসের পাত্র হয়ে উঠল, এবং কী করে সে আমার মেয়ের ভালবাসা আদায় করল, এসব বুঝিয়ে বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে। সে এখানে আসার সময় বিদেশের অনেক জ্ঞানী-গুণীর কাছ থেকে প্রশংসাপত্র নিয়ে এসেছিল; তাই তাকে আমার আমল দিতে হয়। তা ছাড়া তার নিজেরও যে গুণ নেই, তা নয়। তাই শেষ পর্যন্ত আমি খুশি হয়েই তাকে নিয়মিত আমার বাড়িতে আসতে দিই। যখন জানলাম যে আমার মেয়ে এই যুবকের প্রতি আকৃষ্ট, তখন মনে হয়েছিল যে ঘটনাটা যেন একটু বেশি দ্রুত ঘটে গেল। কিন্তু আমি অবাক হইনি, কারণ উইলসনের স্বভাব আর কথাবার্তায় এমন একটা মাধুর্য ছিল যে, সমাজের উঁচু স্তরে নিজের জন্য একটা জায়গা করে নেওয়া তারপক্ষে ছিল সহজ ব্যাপার।
প্রাচ্যের প্রাচীন শিল্পবস্তু সম্পর্কে তার উৎসাহ ছিল, এবং এ বিষয়ে জ্ঞানও ছিল যথেষ্ট। অনেক সময় সন্ধ্যাবেলা আমাদের বাড়িতে সময় কাটাতে এসে সে আমার অনুমতি নিয়ে মিউজিয়মে গিয়ে একা ঘুরে ঘুরে সব দেখত। বুঝতেই পারছেন, এ ব্যাপারে আমি নিজে উৎসাহী হওয়াতে তার অনুরোধে খুশি হয়েই সম্মত হতাম, আর আমার বাড়িতে তার ঘন ঘন আগমনে কোনও বিস্ময় বোধ করতাম না। এলিজের সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ পাকাঁপাকি হয়ে যাবার পর প্রায় প্রতি সন্ধ্যা ছেলেটি আমার বাড়িতে কাটাত, এবং তার মধ্যে ঘণ্টাখানেক কাটাত মিউজিয়মে। সেখানে সে অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করত। এমনকী আমি যেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি থাকতাম না, সেদিনও সে এসে মিউজিয়মে কিছুটা সময় কাটিয়েছে। এই অবস্থার অবসান হয় তখনই, যখন আমি চাকরি ছেড়ে নরউডে চলে যাই, এবং নানা বিষয় নিয়ে বই লেখার তোড়জোড় শুরু করি।
চাকরি ছাড়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই আমি যে লোককে নির্দ্বিধায় আপন করে নিয়েছিলাম, তার আসল চেহারাটা বুঝতে পারি। আমার বিদেশি বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া কয়েকটা চিঠি থেকে আমি জানতে পারি যে, যেসব পরিচয়পত্র উইলসন আমাকে দেখিয়েছিল, তার অধিকাংশই জাল। অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে আমি নিজেকে প্রশ্ন করি, এই ধাপ্পাবাজির পিছনে কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে। সে যদি অর্থলোভী হয়ে থাকে তা হলে আমাকে দিয়ে তার কোনও কাজ হবে না, কারণ আমি ধনী নই। তা হলে সে এল কেন? তখন আমার খেয়াল হল যে, পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান পাথরের বেশ কিছু রয়েছে আমার জিম্মায়, এবং নানান অজুহাতে একা মিউজিয়মে গিয়ে সেসব পাথরের কোষ্টা কোথায় আছে সেটা উইলসন দেখে এসেছে। অর্থাৎ সে হচ্ছে এক অতি ধূর্ত ব্যক্তি, যে আমার মিউজিয়মে চুরির সুযোগ খুঁজছে। এই অবস্থায়, তাকে অন্ধের মতো ভালবাসে আমার যে মেয়ে, তাকে কষ্ট না দিয়ে কী করে আমি উইলসনকে জব্দ করব? আমি অনেক ভেবে যে-পস্থা স্থির করলাম, সেটা বেয়াড়া তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু তার চেয়ে বেশি কার্যকরী কোনও পস্থা আমার মাথায়। এল না। আমি যদি আপনাকে নিজের নামে চিঠি লিখতাম, তখন আপনি নিশ্চয়ই আমাকে নানা খুঁটিনাটি প্রশ্ন করতেন–যার উত্তর আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব হত না। তাই আমি নাম ছাড়াই চিঠি লিখে আপনাকে সতর্ক করে দিই।
আমি বেলমোর স্ট্রিট থেকে নরউড চলে আসার পরেও এই যুবকের আমার বাড়িতে আসা একটুও কমেনি। হয়তো সে সত্যিই আমার মেয়েকে গভীরভাবে ভালবেসেছিল। আর আমার মেয়ের কথা যদি বলেন, তা হলে আমি এটুকু বলব যে, কোনও মেয়ে যে একজন পুরুষের দ্বারা এমনভাবে প্রভাবিত হতে পারে, এটা আমি কল্পনা করতে পারিনি। উইলসনের ব্যক্তিত্ব যেন এলিজকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করেছিল। এটা যে কতদূর সত্যি এবং ওদের দুজনের মধ্যে সম্পর্কটা যে কত গভীর, সেটা আমি বুঝতে পারি এক সন্ধ্যায়, আর তখনই উইলসনের আসল রূপটা ধরা পড়ে। সেদিন আমি আগে থেকে হুকুম দিয়ে রেখেছিলাম যে, উইলসন এলে যেন সোজা আমার কাজের ঘরে চলে আসে বৈঠকখানায় যেন তাকে বসানো না হয়। সে আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি সোজাসুজি বলে দিলাম যে, তার স্বরূপ জানতে আর আমার বাকি নেই, আর সেটা জেনেই তার দুরভিসন্ধির পথ আমি বন্ধ করেছি এবং আমি আর আমার মেয়ে তার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখতে চাই না। সেইসঙ্গে এও বললাম যে, আমার পরম সৌভাগ্য সে মিউজিয়মের মহামূল্য জিনিসগুলোর কোনও ক্ষতি করার আগেই আমি তার আসল পরিচয়টা পেয়ে গেছি।
ছেলেটির বুকের পাটা যে অসামান্য, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আমার কথা সে শেষ পর্যন্ত শুনে কোনও বিস্ময় বা বিরুদ্ধভাব প্রকাশ না করে ঘরের উলটোদিকে গিয়ে ঘন্টা বাজিয়ে চাকরকে ডেকে পাঠাল। চাকর এলে পর তাকে বলল, মিস্ অ্যাড্রিয়াসকে গিয়ে বলো, তিনি যেন অনুগ্রহ করে এখানে আসেন।
আমার মেয়ে এল। উইলসন এগিয়ে গিয়ে তার হাত দুটো নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে বলল, এলিজ, তোমার বাবা এইমাত্র আবিষ্কার করেছেন যে, আমি একটি দুশ্চরিত্র ব্যক্তি–যেটা তুমি আগেই জানতে।
এলিজ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।
উনি বলছেন যে আমাদের পরস্পরকে ত্যাগ করতে হবে, চিরকালের জন্য।
এলিজ কিন্তু এখনও তার হাত ছাড়িয়ে নেয়নি।
তোমার উপর কি আমি ভরসা রাখতে পারি, না কি একমাত্র যে আমাকে সৎপথে চালাতে পারে, সেও আমাকে ছেড়ে চলে যাবে?
জন! আমার মেয়ে গভীর আবেগের সঙ্গে বলে উঠল, আমি কোনওদিন তোমাকে ছেড়ে যাব না। দুনিয়ার সব লোক যদি তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, তা হলেও না।
আমি আমার মেয়েকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোনও ফল হল না। সে যেন এই যুবকটির সঙ্গে তার জীবন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ফেলেছে। আমার মেয়ে আমার চোখের মণি; যখন দেখলাম যে তাকে সর্বনাশের হাত থেকে উদ্ধার করার কোনও উপায় নেই, তখন আমার যে কী অবস্থা হল তা বলতে পারি না। আমার অসহায় ভাব দেখে মনে হল উইলসনের কিছুটা দয়া হল। সে বলল, আপনি যতটা ভাবছেন, অবস্থা ততটা খারাপ নয়। এলিজের প্রতি আমার ভালবাসা এতই গভীর যে, হয়তো সেটাই আমাকে কলঙ্কের হাত থেকে উদ্ধার করবে। আমি কালই ওর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, জীবনে আর কখনও এমন কোনও কাজ করব না যাতে সে কষ্ট। পাবে। কথা দিয়ে কথা না রাখার লোক আমি নই।
উইলসনের কথায় মনে হল সে যা বলছে সেটা অবিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই। কথাটা বলে সে পকেট থেকে একটা কার্ডবোর্ডের বাক্স বার করে বলল, আমি যা বলছি তা যে সত্যি তার প্রমাণ আমি দিতে চাই। এলিজ, আমার উপর তোমার প্রভাব যে মঙ্গলকর সেটা এবার বুঝতে পারবে। প্রোফেসর অ্যান্ড্রিয়াস, আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন যে আপনার সংগ্রহশালার অমূল্য সম্পদ আমাকে প্রলুব্ধ করেছিল। যে কাজে লাভের সম্ভাবনার সঙ্গে বিপদের আশঙ্কা জড়িয়ে থাকে, সে কাজের প্রতি চিরকালই আমি একটা আকর্ষণ বোধ করি, তাই ইহুদির কবচের পাথরগুলোকে হাত করার জন্য আমি বদ্ধপরিকর হই।
সেটা আমি অনুমান করেছিলাম।
কিন্তু একটা ব্যাপার আপনি অনুমান করতে পারেন নি।
কী?
যে সেগুলো হাত করতে আমি সক্ষম হয়েছিলাম। এই বাক্সের মধ্যে রয়েছে সেই পাথরগুলো।
এই বলে সে বাক্সটা খুলে আমার ডেস্কের উপর উপুড় করে ধরল। দৃশ্য দেখে আমার হাত-পা হিম হয়ে এল। সংকেত চিহ্ন আঁকা বারোটা মহামূল্য পাথর বেরিয়ে পড়েছে আমার টেবিলের উপর। এগুলোই যে উরিম ও ঘুমিমের পাথর, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।
সর্বনাশ! আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। তুমি ধরা না পড়ে এ কুকীর্তি করলে কী করে?
আসলের জায়গায় নকল পাথর বসিয়ে, বলল উইলসন, নকলগুলো এতই নিখুঁত যে, দুইয়ের মধ্যে তফাত করা অসম্ভব।
এখন যে পাথরগুলো কবচে লাগানো রয়েছে, সেগুলো নকল?
হ্যাঁ, এবং বেশ কিছুকাল আগেই ঘটেছে এই ঘটনা।
আমরা তিনজন কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার মেয়ের মুখ বিবর্ণ হলেও সে তখনও তার হাত ছাড়িয়ে নেয়নি।
উইলসন এলিজের দিকে ফিরে বলল, আমার সাধ্যের মাত্রা কতদূর সেটা তো এবার বুঝলে?
এলিজ বলল, এটাও বুঝলাম যে দুষ্কর্ম করেছ, তার জন্য অনুতপ্ত হওয়াটাও তোমার অসাধ্য নয়।
সেটা তোমার প্রভাবের ফল বলল উইলসন, আমি পাথরগুলো আপনাকেই দিচ্ছি, প্রোফেসর অ্যাড্রিয়াস। আপনি এ ব্যাপারে যা করা উচিত মনে করবেন, তাই করবেন। কিন্তু মনে রাখবেন, আমার বিরুদ্ধে কিছু করা মানেই আপনার মেয়ের ভবিষ্যৎ স্বামীর বিরুদ্ধে করা। এলিজ, কিছুদিন পরেই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব। এর পরে আর কোনওদিন আমার জন্য তোমাকে কষ্টভোগ করতে হবে না। এই বলে উইলসন প্রস্থান করল।
আমার অবস্থা তখন শোচনীয়। অমূল্য পাথরগুলো এখন আমার হাতে, কিন্তু ধরা না পড়ে কী করে সেগুলো যথাস্থানে ফেরত দিই? এটা বুঝতে পারছি যে, আমার মেয়ে যে রকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাকে উইলসন-এর হাত থেকে কোনওমতেই রক্ষা করতে পারব না। আর উইলসনের প্রভাব যদি তার উপর সত্যিই মঙ্গলকর হয়, তা হলে তাকে রক্ষা করার প্রশ্নই বা আসবে কেন? উইলসনের মুখখাশ খুলে দিলেই বা কী ফল হবে, বিশেষ করে সে যখন আমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে?
আমি অনেক ভেবে একটা রাস্তা বার করলাম, যেটা হয়তো আপনাদের কাছে খুব অবাচীন বলে মনে হবে, কিন্তু আমার মতে এ ছাড়া আর কোনও রাস্তা ছিল না। আমি স্থির করলাম, কাউকে জানতে না দিয়ে আমি নিজেই গিয়ে পাথরগুলো যথাস্থানে বসিয়ে দেব। আমার চাবির সাহায্যে আমি যে কোনও সময় মিউজিয়মে ঢুকতে পারি, আর সিম্পসনের গতিবিধি যখন জানা আছে, তখন ধরা পড়ারও কোনও আশঙ্কা নেই। যা করতে যাচ্ছি সে সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলব না–আমার মেয়েকেও না–এটাও স্থির করলাম। মেয়েকে বললাম, আমি স্কটল্যান্ডে আমার ভাইয়ের কাছে। যাচ্ছি। কটা রাত কারুর সন্দেহ উদ্রেক না করে আমি নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারি, এটাই ছিল আমার লক্ষ্য। সেই রাত্রেই হার্ডিং স্ট্রিটে একটা ঘর ভাড়া করলাম। বাড়িওয়ালাকে বললাম আমি খবরের কাগজে কাজ করি, আমাকে রাত্রেও কাজে বাইরে যেতে হতে পারে।
সেই রাত্রে মিউজিয়মে গিয়ে আমি প্রথম সারির চারটে নকল পাথর খুলে ফেলে আসল পাথর বসিয়ে দিলাম। কাজটা সহজ নয়, এবং সেটা করতে আমার সারারাত লেগে গেল। সিম্পসনের পায়ের শব্দ পেলেই আমি মমি-কেসের মধ্যে লুকিয়ে পড়তাম। স্বর্ণকারের কাজ সম্বন্ধে আমার কিছু জ্ঞান আছে, কিন্তু উইলসন ছিল আমার চেয়ে অনেক বেশি দক্ষ। সে যেভাবে মেকি পাথরগুলো বসিয়েছিল, তাতে সোনার কারুকার্য একটুও রদবদল হয়নি। কিন্তু আমার ছিল কাঁচা এবং বুড়ো হাতের কাজ। আমি চাইছিলাম যে যে-কদিন আমি কাজটা করব, সেকদিন যেন কেউ বেশি মনোযোগ দিয়ে কবচটাকে না দেখে। যাই হোক, একইভাবে দ্বিতীয় রাত্রে দ্বিতীয় সারির পাথরগুলো বসিয়ে ফেললাম। আজ কাজটা শেষ হয়ে যেত, কিন্তু অদৃষ্টের ফেরে সেটা হল না, এবং সেইসঙ্গে আমাকে এমন সব কথা বলে ফেলতে হল, যেগুলো একান্তই গোপনীয়। এখন আপনারা নিজেদের বিদ্যাবুদ্ধি দিয়ে স্থির করুন, এখানেই ঘটনার পরিসমাপ্তি হবে, না এটাকে আরও কিছুদূর টেনে নেবেন। আমার নিজের শান্তি, আমার মেয়ের ভবিষ্যৎ এবং তার ভাবী পতির সংস্কার–সবই নির্ভর করছে আপনাদের সিদ্ধান্তের উপর।
মর্টিমার বলল, সিদ্ধান্ত হল এই যে, যেহেতু সব ভাল যার শেষ ভাল, এই মুহূর্তে সমস্ত ঘটনাটির উপর চিরকালের মতো যবনিকা ফেলে দেওয়া হোক। কালই একজন পাকা স্বর্ণকারকে দিয়ে পাথরগুলো ঠিক করে বসিয়ে কবচটাকে আবার আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হবে। এবারে আপনার হাতটা দিন, প্রোফেসর অ্যাড্রিয়াস, আর আশীবাদ করুন যেন এরকম অবস্থায় যদি কোনওদিন পড়তে হয় আমাকে, আমিও যেন আপনার মতো নিঃস্বার্থ আচরণ করতে পারি।
কাহিনী শেষ করার আগে একটা কথা বলা দরকার। এক মাসের মধ্যেই এলিজের বিয়ে হয়ে গেল তার সঙ্গে যার আসল নামটা বললে পাঠক বুঝতে পারতেন যে, তিনি এখন সমাজে সম্মানিত ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত। কিন্তু সত্যি কথাটা হল এই যে, সম্মান তার চেয়েও বেশি প্রাপ্য সেই শান্তস্বভাবা তরুণীর, যিনি তাঁর স্বামীকে পাপের পঙ্কিল পথ থেকে উদ্ধার করে ভদ্রসমাজে তার স্থান করে দিয়েছিলেন।
দি জু’স ব্রেস্টপ্লেট
সন্দেশ, অগ্রহায়ণ, পৌষ ১৩৯১
ঈশ্বরের ন লক্ষ কোটি নাম
আপনাদের অর্ডারটা একটু অস্বাভাবিক ধরনের, বিস্ময়ের মাত্রাটা যথাসম্ভব কমিয়ে বললেন ডাঃ ওয়াগনার–আমি যতদূর জানি, এর আগে কোনও তিব্বতি গুম্ফা থেকে অটোমেটিক সিকুয়েন্স কম্পিউটারের জন্য অর্ডার আসেনি। আপনাদের ঠিক এই ধরনের মেশিনের প্রয়োজন হতে পারে সেটা আমি ভাবিনি। আপনারা কী কাজের জন্য যন্ত্রটা চাইছেন, সেটা একটু বুঝিয়ে বলবেন কি?
নিশ্চয়ই, তাঁর সিল্কের আলখাল্লাটিকে সামলে নিয়ে, স্লাইড রুলের সাহায্যে ডলার ও তিব্বতি মুদ্রার পারস্পরিক সম্পর্কের হিসাবটা স্থগিত রেখে বললেন লামা। নিশ্চয়ই বলব। আপনাদের মার্ক-৪ কম্পিউটার সবরকম গণনারই কাজ করতে পারে, যদি না একসঙ্গে দশটার বেশি সংখ্যার প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের কাজের জন্য আমরা সংখ্যার কথা ভাবছি না–আমরা ভাবছি অক্ষরের কথা। আপনারা যদি যন্ত্রের সার্কিটে কিছু অদল-বদল করে সেটাকে এমন একটা অবস্থায় এনে দিতে পারেন, যাতে তার সাহায্যে সংখ্যার বদলে অক্ষর ছাপা হবে, তা হলেই আমাদের কাজ হয়ে যায়।
ব্যাপারটা কিন্তু আমার কাছে এখনও ঠিক—
আমরা এই কাজটা বিনা যন্ত্রে গত তিনশো বছর ধরে করে আসছি। অর্থাৎ আমাদের গুম্ফা যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন থেকে। হয়তো কাজটা আপনি এখনও ঠিক অনুধাবন করতে পারছেন না, কিন্তু যদি একটু মন দিয়ে শোনেন, তা হলেই পারবেন।
বেশ তো।
আসলে ব্যাপারটা খুবই সহজ। আমরা একটা তালিকা প্রস্তুত করছি, যাতে ঈশ্বরের যতরকম নাম হয়, তার সবগুলিই থাকবে।
মানে–?
লামা নিরুদ্বিগ্নভাবে বলে চললেন, আমাদের বিশ্বাস, ঈশ্বরের কোনও নাম লিখতেই নটির বেশি অক্ষরের প্রয়োজন হয় না। অবিশ্যি, নাম লিখতে যে বর্ণমালা ব্যবহার হবে, সেটা নতুন এবং আমাদেরই তৈরি।
এই কাজ আপনারা তিনশো বছর ধরে করছেন?
আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা অনুমান করি, কাজটা সম্পূর্ণ হতে লাগত আরও পনেরো হাজার বছর।
ডাঃ ওয়াগনার এখনও খেই পাচ্ছেন না। তিনি বললেন, বুঝলাম। এখন বুঝতে পারছি, কেন আপনারা কম্পিউটার ব্যবহার করার কথা ভাবছেন। কিন্তু এই কাজের আসল উদ্দেশ্যটা কী?
লামার মধ্যে যেন কিঞ্চিৎ ইতস্তত ভাব। ডাঃ ওয়াগনারের আশঙ্কা হল, তিনি বুঝি অজান্তে অপমানসূচক কিছু বলে ফেলেছেন। কিন্তু লামার উত্তরে কোনও বিরক্তি প্রকাশ পেল না।
এই কাজটা আমাদের আচারানুষ্ঠানের একটা অঙ্গ। আমরা এটাকে একটা কর্তব্য বলে মনে করি। যতরকম নামে মানুষ ঈশ্বরকে জানে–গড়, জেহোভা, আল্লা, ইত্যাদি–এগুলো সবই মানুষের দেওয়া নাম। এখানে অবিশ্যি কতগুলো দার্শনিক প্রশ্ন এসে পড়ছে যেগুলো আমি আলোচনা করতে চাই না, কিন্তু নটি অক্ষরে সীমাবদ্ধ রেখে যদি আমরা সেগুলিকে পারমিউটেশন কম্বিনেশনের সাহায্যে পাশাপাশি বসিয়ে চলি, তা হলে আমার বিশ্বাস, শেষ পর্যন্ত আমরা ঈশ্বরের সবকটি নামই লিখে ফেলতে পারব। সেই বিন্যাসের কাজটা আমরা এতদিন যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই করে আসছি।
বুঝেছি–আপনারা AAAAAAAA থেকে শুরু করে ZZZZZZZZZ পর্যন্ত যেতে চান।
ঠিক তাই। যদিও–যে কথাটা বললাম–এক্ষেত্রে অক্ষরগুলো আমরাই তৈরি করেছি। সংখ্যা থেকে অক্ষরে পরিবর্তন করার কাজটা আপনাদের পক্ষে কঠিন হওয়ার কথা নয়। তবে এমন সার্কিট করা দরকার, যাতে অক্ষরগুলো যুক্তিসম্মতভাবে পরপর সাজানো হয়। যেমন, কোনও শব্দে একই অক্ষর পরপর তিনবারের বেশি ব্যবহার করা চলবে না।
তিনবার? না দু বার?
তিনবার। কেন তিনবার সেটা বোঝাতে গেলে বৃথা সময় নষ্ট হবে।
ওঃ, বললেন ডাঃ ওয়াগনার। আর কিছু বলার আছে কি?
আমার বিশ্বাস, আপনাদের যন্ত্রটিকে আমাদের কাজের উপযুক্ত করে তৈরি করে দিতে বেশি সময় লাগবে না। তার পরেই সংখ্যার বদলে অক্ষর-বিন্যাসের কাজটা শুরু হয়ে যেতে পারবে। আমার ধারণা, যে কাজটা আমাদের লাগত পনেরো হাজার বছর, সেটা যন্ত্রের সাহায্যে হয়ে যাবে একশো দিনে।
ডাঃ ওয়াগনারের ঘরের খোলা জানলা দিয়ে নিউ ইয়র্ক শহরের ট্রাফিকের মৃদু গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে, কিন্তু সে শব্দ তাঁর কানে প্রবেশই করছে না। তাঁর মন এখন সম্পূর্ণ অন্য জগতে বিচরণ করছে। যেখানে গগনচুম্বী পাহাড়গুলি প্রকৃতির সৃষ্টি, মানুষের নয়। সেই পাহাড়ের চুড়োয় গুম্ফায় বসে এই তিব্বতি সাধকেরা যুগের পর যুগ ধরে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তাদের অর্থহীন তালিকা তৈরি করে যাচ্ছে! মানুষের পাগলামির কি কোনও সীমা নেই? যাই হোক, তাঁর মনের ভাব বাইরে প্রকাশ করা চলবে না। কথাই তো আছেদ্য কাস্টমার ইজ নেভার রং।
ডাঃ ওয়াগনার বললেন, এটা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে, আমাদের মার্ক-৫ কম্পিউটারকে আপনাদের কাজের উপযুক্ত করে তৈরি করে দিতে পারি আমরা। আমি এখন যে কথাটা ভেবে চিন্তিত হচ্ছি, সেটা হল–আপনাদের গুম্ফাতে যন্ত্রটিকে বসানো, চালানো এবং তার পরিচর্যা নিয়ে। ওটাকে তিব্বতে নিয়ে যাওয়াটাও তো একটা দুরূহ কাজ।
সে ব্যবস্থা আমরা করব। আপনাদের কম্পিউটারের অংশগুলো তেমন কিছু বড় নয়–যে কারণে আপনাদের মডেলটা বাছাই করেছি। ওটাকে একবার ভারতবর্ষে পৌঁছে দিতে পারলে বাকি পথটুকুর ব্যবস্থা আমরাই করব।
আর আপনি বলছিলেন, আমাদের এখান থেকে দুজন লোক নেওয়ার কথা?
হ্যাঁ। তিন মাসের জন্য। তার বেশি সময় নিশ্চয়ই লাগবে না।
সে ব্যবস্থাও হয়ে যাবে, বিষয়টা প্যাডে নোট করে নিয়ে বললেন ডাঃ ওয়াগনার। অবিশ্যি আরও দুটো ব্যাপার–
কথা শেষ করার আগেই লামা তাঁর আলখাল্লার পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে ওয়াগনারের হাতে দিয়ে বললেন, এটা হল এশিয়াটিক ব্যাঙ্কে আমার কত টাকা জমা আছে তার সার্টিফিকেট।
ধন্যবাদ। হ্যাঁ–তা, এতে যথেষ্ট হবে বলেই মনে হয়। দ্বিতীয় ব্যাপারটা এতই মামুলি যে, সেটা উল্লেখ করতেও আমার সঙ্কোচ হচ্ছে–অথচ না করলেও নয়। আপনাদের ইলেকট্রিসিটির কী ব্যবস্থা?
১১০ ভোল্টে ৫০ কিলোওয়াট উৎপাদনকারী ডিজেল জেনারেটর। বছর পাঁচেক হল এটা বসানো হয়েছে এবং কাজ দিচ্ছে ভালই। এটা আসার পর থেকে গুম্ফার জীবনযাত্রা অনেক সহজ হয়ে গেছে। অবিশ্যি ওটা আনার মূল উদ্দেশ্য ছিল বড় বড় জপ-যন্ত্রগুলোকে চালানো।
তা তো বটেই, বললেন ডাঃ ওয়াগনার। এটা আমার অনুমান করা উচিত ছিল।
.
গুম্ফার ছাতের বেঁটে পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে বাইরে নীচের দিকে চাইলে প্রথমে মাথা ভোঁ ভোঁ করে ঠিকই, কিন্তু ক্রমে সবই অভ্যাস হয়ে যায়। এই তিন মাসেও দু হাজার ফুট নীচে খাদের দৃশ্য বা দূরে উপত্যকায় শস্যক্ষেত্রের নানারকম জ্যামিতিক নকশা জর্জ হ্যানলির মনকে নাড়া দিতে পারেনি। সে এখন ছাতের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দূরের পর্বতশৃঙ্গগুলোর দিকে চেয়ে আছে। সেগুলোর নাম জানার কোনও ঔৎসুক্য সে বোধ করেনি। এমন বেয়াড়া অবস্থায় তাকে কোনও দিন পড়তে হয়েছে কি? নিশ্চয়ই না। গত তিন মাস ধরে মার্ক-৫ কম্পিউটারে উদ্ভট অক্ষরের সমষ্টি ছাপা রোলের পর রোল কাগজ বেরিয়ে আসছে। অক্ষরগুলির যতরকম সম্ভাব্য বিন্যাস হতে পারে, যান্ত্রিক টাইপরাইটারে তার প্রত্যেকটি ছেপে চলেছে অক্লান্তভাবে। কাগজের রোল বেরোনোর সঙ্গে। সঙ্গে লামারা প্রত্যেকটি শব্দ কাঁচি দিয়ে কেটে সেগুলোকে বিরাট বিরাট খাতায় সযত্নে সেঁটে ফেলছে। আর এক সপ্তাহে কাজ শেষ হওয়ার কথা। কোন্ হিসাবের ভিত্তিতে যে এরা কথাগুলোকে ন-অক্ষরে সীমাবদ্ধ রেখেছে, তার রহস্য জর্জ হ্যানলির অজানা। একটা আশঙ্কা মাঝে মাঝে হ্যানলির বুক কাঁপিয়ে দেয়, সেটা হল এই যে, লামারা হয়তো হঠাৎ একদিন স্থির করবে যে কাজটা ২০৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চালানো দরকার। এদের পক্ষে সবই সম্ভব।
একটা ভারী কাঠের দরজা খোলার শব্দের সঙ্গে চা ছাতে এসে জর্জের পাশে দাঁড়াল। চাকের মুখে চুরুট–যে চুরুট লামাদের ভারী প্রিয় হয়ে উঠেছে। ধর্মযাজক হলেও এরা অল্পবিস্তর ফুর্তির স্বাদ গ্রহণ করতে বিমুখ নয়। এরা ছিটগ্রস্ত হতে পারে, কিন্তু গোঁড়া নয়।
চাক্ এসেছে একটা জরুরি বক্তব্য নিয়ে। যা শুনছি জর্জ, তাতে কিন্তু ব্যাপার গোলমেলে বলে মনে হচ্ছে।
কী শুনছ? যন্ত্র ঠিকমতো কাজ করছে না? জর্জের মতে এর চেয়ে বেশি গোলমেলের আর কিছু হতে পারে না। যন্ত্রের গণ্ডগোল হলে তাদের যাওয়া পিছিয়ে যেতে পারে, আর সেটাই হবে চরম বিপর্যয়। ইদানীং টেলিভিশনের রদ্দিমাকা বিজ্ঞাপনের ছবিগুলোর কথা ভেবেও জর্জের মন কেমন করে, কারণ সেগুলোও তো দেশের কথাই মনে করিয়ে দেয়!
না না, বলল চাক্, সে ধরনের গোলমাল নয়। চাক সাধারণত ছাতের পাঁচিলে বসে না, কারণ তাতে তার বুক ধড়ফড় করে, কিন্তু আজ ও সেখানেই বসে বলল, আমি আসল ব্যাপারটা জেনে ফেলেছি।
তার মানে? ব্যাপার তো সবই আমাদের জানা।
আমরা যেটা জানি সেটা হল লামারা কী করতে যাচ্ছে, কিন্তু কেন করতে যাচ্ছে, সেটা তো জানতাম না। এখন সেটা জেনেছি, এবং সে এক অভাবনীয় ব্যাপার!
তোমার ওসব বাজে কথা ছাড়া তো?
কিন্তু লামা যে আমায় নিজে বলেছেন! তুমি তো জানো, উনি রোজ এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কম্পিউটার থেকে টাইপ করা কাগজের রোল বেরিয়ে আসা দেখেন। আজও এসেছিলেন এবং আজ কেন যেন অন্যদিনের তুলনায় ওঁকে বেশি উত্তেজিত বলে মনে হচ্ছিল। আমি যখন বললাম যে আমাদের কাজ প্রায় শেষ হতে চলেছে, উনি আমাকে তাঁর অদ্ভুত ইংরিজি উচ্চারণে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা কোনওদিন এই কাজটার পিছনে আসল উদ্দেশ্যটা সম্বন্ধে কিছু অনুমান করেছি কিনা। আমি বললাম–সেরকম উদ্দেশ্য কিছু আছে নাকি? তখন ভদ্রলোক ব্যাপারটা বললেন।
কী বললেন?
এঁরা বিশ্বাস করেন যে, যখন ঈশ্বরের নামের তালিকা তৈরি হয়ে যাবে–এঁদের মতে নামের সংখ্যা হচ্ছে ন লক্ষ কোটি–তখন ঈশ্বরের কাজও ফুরিয়ে যাবে। সেইসঙ্গে মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল যে কাজ করার জন্য, তাও শেষ হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়–এর পরে মানুষের পক্ষে কিছু করতে যাওয়াটাই হবে ঈশ্বরবিরোধী কাজ।
তা হলে আমরা এখন করছিটা কী? আত্মহত্যা?
সেটার প্রয়োজন কোথায়? তালিকা শেষ হলে পর ঈশ্বর নিজেই যা করার করবেন। অর্থাৎ–খেল খতম!
বুঝলাম। আমাদের কাজ শেষ হওয়া মানে পৃথিবীর কাজও খতম!
চাক্ একটা শুকনো হাসি হেসে বলল, আমি ঠিক সেই কথাটাই বলেছিলাম লামাকে। কিন্তু তার ফল কী হল জানো? উনি আমার দিকে একটা অদ্ভুত দৃষ্টি দিয়ে বললেন–ব্যাপারটাকে অত হালকাভাবে নিও না।
জর্জ একটুক্ষণ চিন্তিতভাবে চুপ করে থেকে বলল, কিন্তু এ ব্যাপারে কী করা উচিত, সেটা তো বুঝতে পারছি না। অবিশ্যি সেভাবে দেখতে গেলে যাই করি না কেন তাতে কিছু এসে যায় না। এরা যে বদ্ধ পাগল, সে তো জানাই আছে।
কিন্তু একটা জিনিস ভেবে দেখো জর্জ-তালিকা শেষ হওয়ার পর যদি কিছু না ঘটে, পৃথিবী যেমন আছে তেমনই থেকে যায়, তা হলে দোষটা আমাদের ঘাড়ে পড়বে না তো? আমাদেরই যন্ত্র তো কাজটা করছে! ব্যাপারটা আমার কাছে মোটেই ভাল লাগছে না।
কথাটা খুব ভুল বলোনি, জর্জ গম্ভীরভাবে মন্তব্য করল। কিন্তু এ ধরনের ব্যাপার তো আগেও ঘটেছে। লুইসিয়্যানায় আমাদের ছেলেবেলায় এক ছিটগ্রস্ত পাদরি হঠাৎ একদিন বলে বসলেন–আসছে রবিবার পৃথিবীর শেষ দিন। বহু লোক তাঁর কথা বিশ্বাস করল। এমনকী, সেই বিশ্বাসে তাদের ঘরবাড়ি সব বিক্রি করে দিল। শেষটায় যখন কিছুই হল না, তখন কিন্তু তারা এই নিয়ে কোনওরকম মাতামাতি করল না। তারা ধরে নিল, পাদরির হিসেবে কোনও গণ্ডগোল হয়েছে। আসলে ঘটনাটা ঘটবে ঠিকই, কিন্তু পরে।
যাই হোক, এটা যে লুইসিয়্যানা নয়, সে খেয়াল আশা করি তোমার আছে। এখানে কেবল আমরা দুজন শ্বেতাঙ্গ, বাকি হল তিব্বতি সাধকদের বিরাট দল। এঁরা তোক ভালই এবং সত্যিই যদি। লামার ভবিষ্যদ্বাণী না ফলে, তা হলে আমার ওঁর জন্য একটু কষ্টই হবে। কিন্তু তাও বলছি, এ সময়টা এখানে না থেকে অন্য কোথাও থাকলে আমি নিশ্চিন্ত বোধ করতাম।
সে-কথাটা আমার কিছুদিন থেকে মনে হচ্ছে। কিন্তু আমরা যে চুক্তি সই করেছি। আর আমাদের ফেরত যাবার প্লেন না আসা পর্যন্ত তো আমরা কিছুই করতে পারছি না।
চাক্ চিন্তিতভাবে মাথা নেড়ে সায় দিল। তারপর প্রায় আপনমনেই বলল, অবিশ্যি আমরা ব্যাপারটা ভণ্ডুল করে দিতে পারি।
খেছে? ওতে আরও বিপদ।
আমি যেভাবে ভাবছি, তাতে বিপদ নেই। শোনো-। মেশিন চলবে আর চারদিন–দিনে চব্বিশ ঘণ্টা করে। আমাদের প্লেন আসবে এক হপ্তা পরে। বেশ। এখন ধরো যদি এর মধ্যে যন্ত্রে কোনও গণ্ডগোল হয়, দুদিন কাজ বন্ধ থাকে। গণ্ডগোল আমরা শুধরিয়ে দেব ঠিকই; কিন্তু সেটা করব একেবারে শেষ মুহূর্তে। আমরাও প্লেনে উঠব, আর ঈশ্বরের শেষ নামটিও উঠবে তালিকায়। তখন আমরা লামাদের আওতার বাইবে।
ব্যাপারটা আমার মনঃপূত হচ্ছে না, মাথা নেড়ে বলল জর্জ। এ ধরনের কারচুপি আমার ধাতে নেই ভায়া। তা ছাড়া এতে ওদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে। নাঃ, যেমন চলছে চলুক, তাতে যা হওয়ার হবে।
.
সাতদিন পরে খচ্চরের পিঠে চড়ে প্যাঁচানো রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে জর্জ বলল, আমার এখনও ব্যাপারটা ভাল লাগছে না। এটা ভেবো না যে, আমি ভয় পেয়েছি বলে পালাচ্ছি। আমার এই বুড়ো লামাগুলোর জন্য মমতা হচ্ছে। তারা যখন দেখবে যে, তাদের ভবিষ্যদ্বাণী ফলল না, তখন। তাদের অবস্থা কী হয়, সেটা আমি দেখতে চাই না। আর আমাদের হেড লামার যে কী প্রতিক্রিয়া হবে, কে জানে।
চাক্ বলল, আশ্চর্য। –ওঁকে যখন গুডবাই করলাম, তখন কেন যেন মনে হল যে, উনি আমাদের মনের কথা সব জানেন, কিন্তু তাই নিয়ে কোনও উদ্বেগ বোধ করছেন না, কারণ মেশিন আবার ঠিকমতো চলছে, আর কাজও অল্পক্ষণের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে। তারপর–অবিশ্যি ওঁর মতে তারপর বলে আর কিছু নেই।
জর্জ ঘোড়ার পিঠে উলটোমুখে ঘুরে পাহাড়ের দিকে চাইল। এর পরে মোড় ঘুরে আর গুফাটাকে দেখা যাবে না। সূর্যাস্ত হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। আকাশের শেষ রঙের সামনে বিরাটাকৃতি গুফাটাকে দেখা যাচ্ছে। কালো প্রাসাদের গায়ে এখন সেখানে জানলার ভিতরে আলো, যেমন দেখা যায় সমুদ্রগামী জাহাজের গায়ে পোর্টহোলের ভিতরে। ওগুলো সবই জেনারেটর চালিত বৈদ্যুতিক আলো, এবং একই জেনারেটরে চলছে কম্পিউটার। আর কতক্ষণ চলবে যন্ত্র? ভবিষ্যদ্বাণী না। ফললে লামারা কি তাদের আক্রোশ প্রকাশ করবে ওই যন্ত্রকে ধ্বংস করে? না কি তারা আবার নিরুদ্বেগে শুরু করবে তাদের হিসাব?
গুম্ফায় ঠিক এই মুহূর্তে কী হচ্ছে সেটা অবিশ্যি জর্জের জানতে বাকি নেই। লামাপ্রবর তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে যন্ত্রটার কাছে বসে আছেন। অপেক্ষাকৃত কমবয়স্করা তাঁদের সামনে এনে হাজির করছে যন্ত্র থেকে নতুন বেরিয়ে-আসা নামের তালিকা। লামারা নামগুলোর উপর চোখ বোলাচ্ছেন, তারপর সেগুলো কেটে কেটে খাতায় সেঁটে ফেলছেন। কারও মুখে কোনও কথা নেই, একমাত্র শব্দ হচ্ছে যান্ত্রিক টাইপরাইটারের, কারণ মার্ক-৫ কম্পিউটার প্রতি সেকেন্ডে হাজার হিসাবের কাজ করে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে। জর্জ ও চাক্ তিন মাস ধরে এই কাজ দেখেছে। তাদের যে মাথা খারাপ হয়ে যায়নি, এটা পরম ভাগ্যি।
ওই দেখো, বলে উঠল চা সামনের উপত্যকার দিকে হাত বাড়িয়ে। আহা, কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে বলো তো!
জর্জ মনে মনে ভাবল–সত্যিই সুন্দর। পুরনো ডি-সি-থ্রি বিমানটা রানওয়ের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে একটি রুপালি ক্রুশের মতো। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ওদের দুজনকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে সভ্য জগতে, যেখানে তারা পাবে মুক্তি। উৎকৃষ্ট সুরাপানে যে আনন্দ হয়, চিন্তাটা মাথায় আসতে জর্জ সেই আনন্দ অনুভব করল।
হিমালয়ের হঠাৎ-রাত্রি এখনই তাদের গ্রাস করবে। তবে সৌভাগ্যক্রমে রাস্তা ভাল, আর দৃজনের কাছেই রয়েছে টর্চ। একমাত্র যদি না শীত হঠাৎ বেড়ে গিয়ে অস্বস্তির কোনও কারণ ঘটায়, এ ছাড়া কোনও চিন্তা নেই। মাথার উপরে মেঘমুক্ত আকাশে অগণিত অতি পরিচিত নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে। জর্জের একমাত্র দুশ্চিন্তা ছিল যে, প্রতিকূল আবহাওয়ার জন্য হয়তো প্লেন না উড়তে পারে; কিন্তু এখন সে দুশ্চিন্তাও দূর হয়েছে।
জর্জের গলা দিয়ে গান বেরিয়ে এল; তবে বেশিক্ষণের জন্য নয়। পর্বত পরিবেষ্টিত এই বিশাল প্রান্তরে গানটা যেন কিঞ্চিৎ বেমানান। সে রিস্টওয়াচের দিকে চাইল।
আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া উচিত, সে চেঁচিয়ে জানাল পিছনে চাক-এর উদ্দেশে। তারপর আরও কতগুলো কথা সে জুড়ে দিল। কম্পিউটারের কাজ শেষ হল কিনা কে জানে। এখনই তো হওয়ার কথা।
চাক-এর কাছ থেকে কোনও উত্তর না পেয়ে জর্জ উলটোমুখে ঘুরল। সে দেখল ঘোড়ার পিঠে চাককে–তার দৃষ্টি আকাশের দিকে।
ওপরে চেয়ে দেখো, বলল চাক্।
জর্জ চাইল –হয়তো শেষবারের মতো।
মাথার উপরে সন্ধ্যার আকাশ থেকে নির্বিবাদে একটি একটি করে তারা মুছে যাচ্ছে।
দি নাইন বিলিয়ন নেমস্ অফ গড
সন্দেশ, কার্তিক ১৩৯১
ব্রেজিলের কালো বাঘ
মেজাজটা বনেদি, প্রত্যাশা অসীম, অভিজাত বংশের রক্ত বইছে ধমনীতে, অথচ পকেটে পয়সা নেই, রোজগারের কোনও রাস্তা নেই–একজন যুবকের পক্ষে এর চেয়ে দৃভাগ্য আর কী হতে পারে? আমার বাবা ছিলেন সহজ, সরল মানুষ। তাঁর দাদা, অকৃতদার লর্ড সাদারটন, বিশাল সম্পত্তির মালিক। এই দাদার বদান্যতার উপর বাবার এমনই আস্থা ছিল যে তাঁর একমাত্র সন্তান হয়ে আমার যে কোনওদিন অন্নসংস্থানের চিন্তা করতে হবে এটা তিনি ভাবতে পারেননি। তাঁর ধারণা ছিল, হয় সাদারটনের বিস্তীর্ণ জমিদারি এস্টেটে, না হয় নিদেনপক্ষে সরকারের কূটনৈতিক বিভাগে আমার। একটা স্থান হবেই। তাঁর অনুমান যে সম্পূর্ণ ভুল সেটা তাঁর অকালমৃত্যুর ফলে বাবা আর জেনে যেতে পারেননি। যেমন আমার জ্যাঠা, তেমনই ব্রিটিশ সরকার, আমার সংগতির জন্য কিছুই করলেন না, বা আমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনও তাপ উত্তাপ প্রকাশ করলেন না। কচিৎ কদাচিৎ কিছু ফেজান্ট পাখি বা গুটিকয়েক খরগোশ উপঢৌকন হিসেবে জ্যাঠার কাছ থেকে আসে, আর সেই থেকেই বোঝা যায় যে আমি ইংল্যান্ডের অন্যতম সবচেয়ে সমৃদ্ধ জমিদারিতে অবস্থিত অটওয়েল প্রাসাদের উত্তরাধিকারী। যাই হোক, আমি নিজে বিয়ে করিনি, লন্ডনের গ্রোভনর ম্যানসনসে ঘর নিয়ে নাগরিক জীবন যাপন করি। কাজের মধ্যে আছে পায়রা শিকার ও হার্লিং হ্যামে পোলা খেলা। আমার ঋণ যে মাসে মাসে বেড়েই চলেছে, কিছুদিন পরে আর তা শোধ করার কোনও উপায়ই থাকবে না, এটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।
আমার এই শোচনীয় অবস্থাটা আরও প্রকট হয়ে উঠছে এই কারণেই যে লর্ড সাদারটন ছাড়াও আমার আরও বেশ কয়েকজন ধনী আত্মীয় রয়েছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে নিকট হলেন আমার খুড়তুতো ভাই এভারার্ড কিং। বেশ কিছুদিন ব্রেজিলে অ্যাডভেঞ্চারপূর্ণ জীবন কাটিয়ে সে সম্প্রতি দেশে ফিরে দিব্যি গুছিয়ে বসেছে। তার উপার্জনের পন্থাটা কী সেটা আমার জানা নেই, তবে তার। অবস্থা যে রীতিমতো সচ্ছল সেটা বোঝা যায়ই, কারণ সে এখন সাফোকের ক্লিণ্টন-অন-দ্য-মার্শে গ্রেল্যান্ডসের জমিদারির মালিক। ইংল্যান্ডে আসার পর প্রথম বছরটা সে আমার কঞ্জুস জ্যাঠার মতোই আমার কোনও খোঁজখবর নেয়নি, কিন্তু এক গ্রীষ্মের সকালে মনটা খুশিতে ভরে উঠল, যখন দেখলাম, সে একটি চিঠি মারফত গ্রেল্যান্ডস কোর্টে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আসার জন্য আমায় আমন্ত্রণ জানিয়েছে। আমি তখন দেউলে হবার আশঙ্কায় অন্যরকম কোর্টে যাবার কথা ভাবছিলাম, আর ঠিক সেই সময় দৈবক্রমে এসে গেল এই চিঠি। আমার এই অচেনা ভাইটিকে যদি হাত করতে পারি, তা হলে হয়তো একটা উদ্ধারের পথ পেলেও পেতে পারি। অন্তত বংশমর্যাদার খাতিরেও তো তার আমাকে পথে বসতে দেওয়া উচিত নয়। চাকরকে বলে আমার বাক্স গুছিয়ে নিয়ে সেইদিনই সন্ধ্যায় আমি ক্লিপটন-অন-দ্য-মার্শের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম।
ইপসিচে গাড়ি বদল করে একটি লোক্যাল ট্রেন আমাকে অসমতল তৃণপ্রান্তরের মাঝখানে একটি জনবিহীন ছোট্ট স্টেশনে নামিয়ে দিল। আমার জন্য কোনও গাড়ি আসেনি (পরে জেনেছিলাম আমার টেলিগ্রাম পৌঁছতে দেরি হয়েছিল), তাই আমি কাছেই একটি পান্থনিবাস থেকে একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে রওনা দিয়ে দিলাম। গাড়ির সহিস দিব্যি লোক–সে আমার ভাইয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বুঝলাম এ অঞ্চলে এর মধ্যেই এভারার্ড কিং-এর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় স্কুলের ছেলেমেয়েদের জন্য সে পার্টি দিয়েছে, জনসাধারণ যাতে তার বিস্তীর্ণ বাগান ঘুরে দেখতে পারে তার ব্যবস্থা করেছে, নানান জনহিতকর কাজে সে অর্থসাহায্য করেছে। মোটকথা, এতভাবে সে তার দরাজ মনের পরিচয় দিয়েছে যে, আমার সহিসের ধারণা হয়েছে, সে পালামেন্টে পদক্ষেপ করার জন্য জমি তৈরি করছে।
পথে যেতে যেতে সহিসের দিক থেকে আমার দৃষ্টি হঠাৎ চলে গেল এক বিচিত্রবর্ণ পাখির দিকে। রাস্তার ধারে টেলিগ্রাফ পোস্টের উপর বসেছে পাখিটা। প্রথমে মনে হয়েছিল বুঝি নীলকণ্ঠ জাতীয় কোনও পাখি, কিন্তু কাছে আসতে দেখলাম আয়তনে তার চেয়ে বেশ খানিকটা বড়, আর পালকে রঙের বাহারও অনেক বেশি। সহিস বলল, আমরা যে ব্যক্তির কাছে চলেছি, এটা তাঁরই পাখি। ইনি নাকি দক্ষিণ আমেরিকা থেকে নানারকম পশুপাখি এনে এখানকার আবহাওয়ায় সেগুলো প্রতিপালনের চেষ্টা করছেন। গ্রেল্যান্ডস পার্কের গেট দিয়ে প্রবেশ করার পর এই কথার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেল। ছোট ছোট বুটিদার হরিণ, এক ধরনের শুয়োর-জাতীয় জানোয়ার–নাম বোধহয় পেকারি–একটি ঝলমলে রঙ বিশিষ্ট ওরিয়োল পাখি, এক শ্রেণীর পিপীলিকাভুক, আর একরকম স্কুল ব্যাজার-জাতীয় জানোয়ার চোখে পড়ল গাছপালায় ঘেরা আঁকাবাঁকা পথটা দিয়ে যেতে।
আমার খুড়তুতো ভাইটি গাড়ির শব্দ পেয়ে আমি এসেছি বুঝে বাড়ির বাইরে সিঁড়িতে এসে দাঁড়িয়ে। ছিল। চেহারায় একটা অমায়িক ভাব ছাড়া তেমন কোনও বিশেষত্ব নেই। আকারে বেঁটে ও মোটা, বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ, রোদে পোড়া গোল মুখে অজস্র বলিরেখা। পরনে সাদা লিনেনের জামা–যেমন প্লান্টাররা পরে থাকে-মুখে চুরুট ও মাথায় পানামা টুপি। দেখে মনে হয় ইনি। প্রাচ্যের কোনও উপনিবেশের বাংলো বাড়ির বাসিন্দা, ইংল্যান্ডের এই সুউচ্চ পালাডিও স্তম্ভ-বিশিষ্ট সুবিশাল অট্টালিকায় ইনি বেমানান।
শুনছ! ভদ্রলোক ঘাড় ফিরিয়ে অদৃশ্য কাউকে উদ্দেশ করে বলেন, উনি এসে গেছেন–আমাদের অতিথি! গ্রেল্যান্ডসে তোমায় স্বাগত জানাচ্ছি, মাশাল ভায়া! তোমার সঙ্গে আলাপের সুযোগে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই ঘুমিয়ে-আসা পল্লী গ্রামে আমার এই বাসস্থানে তোমার যে পায়ের ধুলো পড়ল তাতে আমি সত্যিই সম্মানিত বোধ করছি।
তাঁর এই সাদর অভ্যর্থনায় মুহূর্তের মধ্যে আমার সব সঙ্কোচ কেটে গেল। আর এটার প্রয়োজন ছিল একান্তভাবেই, কারণ স্বামীর ডাকে যে বিবর্ণ, দীঘাঙ্গিনীটি বেরিয়ে এলেন, তাঁর আচরণ অস্বাভাবিক রকম রূঢ়। আমার ধারণা হল ইনি ব্রেজিলের মেয়ে, যদিও ইংরাজিটা বলেন ভালই। হয়তো আমাদের দেশের আদবকায়দার সঙ্গে পরিচয়ের অভাবই তাঁর এই রুক্ষস্বভাবের কারণ। তাঁর আচরণ থেকে এটা পরিষ্কার বুঝতে পারলাম যে, গ্রেল্যান্ডস কোর্টে আমার উপস্থিতিতে তিনি আদৌ প্রসন্ন নন। তাঁর কথায় কোনও অশালীনতার পরিচয় না পেলেও, তাঁর ভাবব্যঞ্জক চোখের চাহনিই স্পষ্ট বুঝিয়ে দিচ্ছিল যে, আমি লণ্ডনে ফিরে না যাওয়া অবধি তাঁর শান্তি নেই।
কিন্তু আমার ঋণের ভার এত বেশি, এবং আমার এই ধনী আত্মীয়টি আমার ত্রাণকতার ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, এ সম্পর্কে আমি এতই আস্থাবান যে, আমি স্ত্রীর রূঢ়তা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে স্বামীর হৃদ্যতার ষোলো আনা সুযোগ নেওয়া স্থির করলাম। আমার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দেখলাম তাঁর সজাগ দৃষ্টি। যে ঘরটি আমায় দেওয়া হয়েছে সেটি চমৎকার। তা সত্ত্বেও ভদ্রলোক বারবার বললেন আমার সুবিধার জন্য যা কিছু দরকার তা তিনি করতে রাজি আছেন। আমি প্রায় বলেই ফেলেছিলাম সবচেয়ে সুবিধা হয় কিছু অর্থসমাগম হলে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল সেটার সময় এখনও আসেনি। নৈশভোজের ব্যবস্থা ছিল পরিপাটি, আর ভোজনান্তে ছিল হাভানা চুরুট আর কফির ব্যবস্থা। চুরুট নাকি তাঁর নিজের বাগানের তামাক থেকে তৈরি। আসার পথে সহিস যা বলছিল তা যে একটুও বাড়িয়ে বলা নয় সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। এঁর মতো মহানুভব, অতিথিবৎসল ব্যক্তি আমি আর দুটি দেখিনি।
কিন্তু এই ব্যক্তির মধ্যেও যে একটি আত্মম্ভর অগ্নিগর্ভ মানুষ বাস করে তার পরিচয় পেলাম পরদিন সকালে। কিং গৃহিণী আমার প্রতি এতই বিমুখ যে, প্রাতরাশের সময় সেটা প্রায় সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। স্বামী ঘর থেকে বেরোনোমাত্র তাঁর মনের ভাবটা পরিষ্কার ফুটে বেরোল।
লণ্ডন ফিরে যাবার সবচেয়ে ভাল ট্রেন হচ্ছে দুপুর সাড়ে বারোটায়, হঠাৎ বললেন ভদ্রমহিলা।
আমি খোলাখুলি বললাম, আমি কিন্তু আজ ফেরার কথা ভাবছি না।
এই মহিলার দ্বারা বিতাড়িত হবার কোনও বাসনা ছিল না আমার।
আপনার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপরই যদি সেটা নির্ভর করে– কথাটা শেষ না করে অত্যন্ত উদ্ধতভাবে ভদ্রমহিলা চাইলেন আমার দিকে।
আমিও ছাড়বার পাত্র নই। বললাম, আমার বিশ্বাস এভারার্ড যদি মনে করে আমি তার আতিথেয়তার অন্যায় সুযোগ নিচ্ছি তা হলে সে কথা সে নিশ্চয়ই আমাকে বলবে।
ব্যাপার কী?
ঘরে ফিরে এসেছে এভারার্ড। মনে হল আমার কথাগুলো সে শুনেছে, এবং আমাদের দুজনের দিকে চেয়ে সে পরিস্থিতিটা আঁচ করে নিয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে তার খুশিতে ভরা গোল মুখটায় এক
অনির্বচনীয় হিংস্রভাব ফুটে উঠল।
তুমি একটু বাইরে যাবে কি, মাশাল? (আমার নাম যে মাশাল কিং সেটা এইবেলা বলে রাখি)।
আমি বেরোতে আমার পিছনের দরজাটা বন্ধ করে দিল এভারার্ড, আর তারপরেই শুনলাম তীব্র ভর্ৎসনার সুরে সে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছে। আতিথেয়তার অবমাননায় সে যে গভীরভাবে ক্ষুব্ধ তাতে সন্দেহ নেই। আড়ি পাতার কোনও অভিসন্ধি ছিল না আমার, তাই আমি বারান্দা থেকে নেমে এলাম বাগানে! কিছুক্ষণ পরে দ্রুত পায়ের আওয়াজ শুনে ঘুরে দেখি মহিলা বাইরে বেরিয়ে এসেছেন, তাঁর মুখ বিবর্ণ, দৃষ্টি বিস্ফারিত।
আমার স্বামী আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে বললেন, মিঃ মাশাল, দৃষ্টি না তুলে বললেন মহিলা।
আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, দোহাই মিসেস কিং, এ নিয়ে আর কিছু বলবেন না।
তাঁর কালো চোখদুটো হঠাৎ ঝলসে উঠল।
মূর্খ!
চাপা অথচ তীক্ষ্ণ স্বরে কথাটা বলে সদর্পে ঘরের ভিতর চলে গেলেন মহিলা।
অপমানটা এতই অপ্রত্যাশিত, এত অসহ্য যে, আমি হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলাম দরজার দিকে। এমন সময় এভারার্ড এল বারান্দায়।
আশা করি আমার স্ত্রী তার অবাচীন ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চেয়েছে তোমার কাছে।
হ্যাঁ, হ্যাঁ–চেয়েছেন বইকী! এভারার্ড কনুইটাকে তার হাতে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল।
তুমি ব্যাপারটা গায়ে মেখে না, বলল এভারার্ড। তোমার মেয়াদের একটি ঘণ্টাও কম যদি থাকো তুমি এখানে তা হলে আমি অত্যন্ত দুঃখ পাব। ব্যাপারটা হচ্ছে কী–ভাইয়ের কাছে গোপন করার কোনও মানে হয় না–আমার স্ত্রী অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণ। আমাদের দুজনের মাঝখানে কেউ এসে দাঁড়ালেই সেটা ও আর বরদাস্ত করতে পারে না, তা সে লোক পুরুষই হোক আর মহিলাই হোক। ও সবচেয়ে কীসে খুশি হয় জানো?–স্বামী-স্ত্রীতে সমুদ্রের মাঝখানে কোনও জনবিহীন দ্বীপে বসে গল্প করে যদি বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিই, তা হলে। এর থেকেই বুঝতে পারবে ও মানুষটা কেমন। আসলে এটা একটা ব্যারামের শামিল। তুমি কথা দাও, এ নিয়ে আর চিন্তা করবে না।
মোটেই না।
তা হলে এই চুরুটটা ধরিয়ে আমার সঙ্গে এসো। আমার পশুসংগ্রহটা দেখাই তোমাকে।
সারা বিকেলটা কেটে গেল এই কাজে। বাইরের থেকে আনা যত পাখি, যত সরীসৃপ, সবই দেখা হল। এদের মধ্যে কিছু রয়েছে খাঁচায়, কিছু খাঁচার বাইরে, আর কিছু একেবারে বাড়ির ভিতর ছাড়া-অবস্থায়। চলতে চলতে সামনে ঘাস থেকে হঠাৎ কোনও রঙব্রেঙের পাখি লাফিয়ে উঠতে দেখে, বা কোনও অচেনা জানোয়ারকে ঝোঁপের আড়ালে লুকিয়ে পড়তে দেখে ছেলেমানুষের মতো উল্লসিত হয়ে উঠছিল এভারার্ড। সবশেষে প্রাসাদের এক প্রান্তে একটি লম্বা প্যাসেজের ভিতর গিয়ে পৌঁছলাম আমরা। প্যাসেজের শেষ মাথায় একটি খড়খড়ি লাগানো ভারী দরজা, আর তার পাশেই একটা হাতল লাগানো চাকা। সেইসঙ্গে লক্ষ করলাম, লোহার ফ্রেমে লাগানো এক সারি খাড়াখাড়ি লোহার শিক দাঁড়িয়ে রয়েছে প্যাসেজের ভিতর।
এবার যেটা দেখাব সেটা হল আমার সংগ্রহের একেবারে সেরা জিনিস, বলল এভারার্ড। ইউরোপে আর একটিমাত্র নমুনা আছে এই জিনিসের। রটারড্যামে একটা বাচ্চা ছিল, সেটা মরে গেছে। জিনিসটা হল একটা ব্রেজিলিয়ান বাঘ।
তার সঙ্গে অন্য বাঘের তফাত কোথায়?
সেটা এখুনি দেখতে পাবে, হেসে বলল কিং। খড়খড়িটা তুলে একবার ভিতরে দেখবে কি?
দরজার গায়ের খড়খড়ি ফাঁক করে চোখ লাগাতেই দেখলাম একটি বেশ বড় ঘর। তার মেঝেতে পাথর বসানো, তার দেয়ালের উপর দিকে শিক দেওয়া ছোট্ট জানলা। ঘরের মাঝখানে মেঝের উপর বসে রোদ পোয়াচ্ছে একটি জানোয়ার। সেটা বাঘের মতোই বড়, যদিও গায়ের রঙ কুচকুচে কালো। আয়তন বিশাল হলেও ভঙ্গিটা দেখে পোষা বেড়ালের কথাই মনে হয়। তার দেহের সুঠাম, পেশল গড়ন, বীর্যের সঙ্গে কমনীয়তার আশ্চর্য সমাবেশ, আমাকে এমন মুগ্ধ করল যে, আমি জানোয়ারের দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারছিলাম না।
জাঁদরেল জানোয়ার, নয় কি? প্রশ্ন করল এভারার্ড।
নিঃসন্দেহে, বললাম আমি। এমন আশ্চর্য জানোয়ার দেখিনি কখনও।
কেউ কেউ এটাকে পুমা বলে। কিন্তু আসলে এটা মোটেই পুমা নয়। এটা মাথা থেকে লেজের ডগা অবধি আঠারো ফুট। চার বছর আগে এটা ছিল দুটো ড্যাবড্যাবে হলদে চোখ বসানো একটি কালো পশমের বল। রিও নিগ্রো নদীর কাছে এক আদিম অরণ্যে একজন এটা বিক্রি করেছিল আমাকে, মা-টাকে বল্লম দিয়ে মেরে ফেলে, যদিও তার আগে এগারোটি মানুষ গেছে তার পেটে।
তার মানে এরা বুঝি খুব হিংস্র হয়?
এমন শয়তান, এমন রক্তপিপাসু জানোয়ার আর দুটি নেই। দক্ষিণ আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের এই বাঘের কথা বললে দেখবে তারা কীরকম চমকে ওঠে। এই জানোয়ারের চেয়ে মানুষের উপর তাদের বিশ্বাস অনেক বেশি। ইনি এখনও মানুষের রক্তের স্বাদ পাননি, কিন্তু একবার পেলে এর চেহারাই বদলে যাবে। এখন পর্যন্ত আমাকে ছাড়া আর কাউকে বরদাস্ত করে না ওর ঘরে। ওর পরিচর্যা করে যে লোক বল্ডউইন–সেও ওর কাছে যেতে সাহস পায় না। ওর বাপ, মা দুই-ই হচ্ছি আমি।
কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে ও আমাকে চমকে দিয়ে দরজাটা খুলে ভিতরে ঢুকে আবার তৎক্ষণাৎ সেটা বন্ধ করে দিল। তার কণ্ঠস্বর শুনে বিশাল জানোয়ারটা উঠে দাঁড়িয়ে হাই তুলে নিজের মাথাটা এভারার্ডের গায়ে ঘষতে লাগল, আর এভারার্ডও জানোয়ারটার গায়ে হাত বুলোতে লাগল।
এবার দেখি টমি বাবু, খাঁচায় ঢোকো তো!
আদেশ শোনামাত্র কৃষ্ণকায় জীবটি ঘরের একপাশে গিয়ে একটি গরাদের ছাউনির তলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে বসল। তারপর এভারার্ড বাইরে এসে হাতলটা ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে প্যাসেজে বেরিয়ে থাকা ফ্রেমবদ্ধ লোহার শিকের সারি দেয়ালের একটা ফাটল দিয়ে বাঘের ঘরে ঢুকে ছাউনির সঙ্গে লেগে গিয়ে দিব্যি একটি খাঁচার সৃষ্টি করল। এবার এভারার্ড দরজা খুলে আমাকে ভিতরে ডাকল। এই বিশেষ শ্রেণীর পদের ঘরে যে বিশেষ গন্ধ পাওয়া যায়, এই ঘর এখন সেই গন্ধে ভরপুর।
এটাই ব্যবস্থা, বলল এভারার্ড। দিনের বেলা ও সমস্ত ঘরটাতেই পায়চারি করে, রাত্রে একপাশে খাঁচাটায় পুরে দেওয়া হয়। বাইরে থেকে হাতল ঘোরালেই খাঁচার দেয়াল সরে গিয়ে ও ছাড়া পেয়ে যায়। আর যদি তা না চাও তো ওকে ওইভাবেই বন্দি করে রাখতে পারো। উহঁ উ ওরকম কোরো না।
আমি গরাদের মধ্যে দিয়ে হাত ঢুকিয়ে বাঘের গায়ে রাখতে গিয়েছিলাম, সে এক হ্যাঁচকা টানে। আমার হাতটা বার করে আনল।
ওকে বিশ্বাস নেই। আমি যা করি, আর পাঁচজনের তা করা চলে না। সবাইকে ও বন্ধু বলে মানতে রাজি নয়। তাই না টমি? হুঁ, এবারে লাঞ্চের গন্ধ পেয়েছেন বাবু। তাই না, টমি?
বাইরে প্যাসেজে পায়ের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বাঘটা এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে অপরিসর খাঁচাটার মধ্যে পায়চারি শুরু করে দিয়েছে। তার হলুদ চোখের চাহনি তীক্ষ্ণ ও অস্থির, তার লেলিহান জিভ বেরিয়ে পড়েছে হাঁ করা মুখের অসমান দাঁতের সারির ফাঁক দিয়ে। একজন পরিচারক পাত্রে একটি মাংসখণ্ড নিয়ে ঘরে এসে গরাদের মধ্যে দিয়ে সেটাকে খাঁচার ভিতর গলিয়ে দিল। বাঘ থাবা দিয়ে আলতো করে সেটাকে তুলে নিয়ে খাঁচার এক কোণে বসে সেটার সদ্ব্যবহার করতে শুরু করল। মাংস টেনে ছেঁড়ার ফাঁকে ফাঁকে সে রক্ত মাখা মুখটা তুলে আমাদের দিকে চাইছে। আমিও একদৃষ্টে দেখছি এই বন্য দৃশ্য।
টমির উপর আমার টানের কারণটা বুঝলে তো? ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করল এভারার্ড। হাজার হোক, আমার হাতেই তো ও মানুষ। কম ঝক্কি গেছে ওকে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে এখানে আনতে? অবিশ্যি এখানে এসে ও ভালই আছে। যা বলছিলাম, এই বিশেষ বাঘের এর চেয়ে ভাল নমুনা ইউরোপে আর নেই। চিড়িয়াখানার কর্তারা একে নেবার জন্য ঝুলোঝুলি করছে। কিন্তু আমি ওকে ছাড়ছি না। যাক গে, আমার মনের কথা ঢের বলা হল, এবার চলো টমির মতো আমরাও গিয়ে লাঞ্চ করি।
দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আসা আমার এ ভাইটি তার জন্তুজানোয়ার নিয়ে এতই মশগুল যে, সে-জগতের বাইরে যে আর একটা জগৎ থাকতে পারে সেটা ভাবাই মুশকিল। কিন্তু সেটা যে রয়েছে সেটা বুঝতে পারতাম তার পাওয়া টেলিগ্রামের বহর থেকে। দিনের যে কোনও সময় আসত এই টেলিগ্রাম, আর তার প্রত্যেকটি অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে খুলত এভারার্ড নিজেই। একেকবার মনে। হত সেগুলো হয়তো ঘোড়ার মাঠ বা স্টক মার্কেট সংক্রান্ত কোনও খবর। মোট কথা, এটা বোঝাই যেত যে এমন কিছু কারবারের সঙ্গে সে জড়িত রয়েছে যেটা ঘটছে সাফোকের বাইরে। আমি যে, ছদিন ছিলাম তার মধ্যে দিনে চারখানা করে টেলিগ্রাম তো এসেইছে, একদিন এল সাতখানা।
এই ছদিন এত ভালভাবে কেটেছে যে ভাইয়ের সঙ্গে একটা চমৎকার সমঝোতা হয়ে গিয়েছিল। প্রতি রাতে বিলিয়ার্ড রুমে বসে এভারার্ড তার আশ্চর্য ভ্রমণকাহিনী শোনাত আমাকে। শুনে বিশ্বাস করা বেশ কঠিন হত যে, আমার এই নিরীহ ভাইটিই এইসব রোমহর্ষক ঘটনার নায়ক। তার। অভিজ্ঞতার পরিবর্তে আমি তাকে শোনাতাম গ্রোভনর ম্যানসনসের জীবনযাত্রার খবর। তাতে সে এতই মুগ্ধ হত যে, বারবার বলত একবার লন্ডনে এসে আমার বাসস্থানে কটা দিন কাটিয়ে যাবে। লন্ডনের চঞ্চল জীবনযাত্রা সম্বন্ধে দেখতাম তার একটা অদম্য কৌতূহল রয়েছে। বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে আমার চেয়ে ভাল গাইড সে পাবে না।
শেষ দিনে আমি আর কথাটা না বলে পারলাম না। সরাসরি বলে দিলাম যে আমার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, এবং সম্পূর্ণ দেউলে হতে আমার আর বেশিদিন বাকি নেই। আমি যদিও তার কাছে পরামর্শই চাইলাম, যেটা আসলে দরকার ছিল সেটা হল বেশ খানিকটা ক্যাশ টাকা।
কিন্তু তুমিই তো লর্ড সাদারটনের উত্তরাধিকারী, তাই না? প্রশ্ন করল এভারার্ড।
আমার তো তাই ধারণা, কিন্তু তিনি আমাকে এক কপর্দকও দেননি কখনও।
জানি, বলল এভারার্ড। সে যে কত কঞ্জুস সে কথা আমি শুনেছি। সত্যি তো, তোমার অবস্থা বেশ কাহিল বলে মনে হচ্ছে। ভাল কথা, সাদারটনের স্বাস্থ্য এখন কেমন?
ছেলেবেলা থেকেই তো শুনে আসছি সে অত্যন্ত রুগ্ণ।
হুঁ…তাও ট্যাঙস ট্যাঙস করে চালিয়ে যাচ্ছে। বেচারা তুমি!
আমার বড় আশা ছিল তুমি সব শুনে-টুনে হয়তো কিছু—
আর বলতে হবে না, হেসে বলল এভারার্ড। আজ রাত্রে এ-বিষয়ে কথা হবে। আমার পক্ষে যতটা সম্ভব করব, কথা দিচ্ছি।
আমার যে বিদায় নেবার সময় এসে গেছে তাতে আমার আক্ষেপ নেই, কারণ জানি যে এ বাড়িরই একজন বাসিন্দা আমাকে তাড়াতে পারলে বাঁচে। কিং গৃহিণীর বিষদৃষ্টি আমার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে। তিনি যে আগ বাড়িয়ে আমাকে অপমান করেন তা নয়; সেখানে স্বামীর ভয় তাঁকে বেশিদূর এগোতে দেয় না। কিন্তু চরম ঈষার বশে তিনি আমার সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিয়েছেন, এবং গ্রেল্যান্ডসে আমার অবস্থান যাতে সবদিক দিয়ে অস্বস্তিকর হয়, সে চেষ্টার কোনও ত্রুটি করেন না। বিশেষত শেষ দিনে তাঁর ব্যবহার এমনই বাড়াবাড়ির পর্যায়ে চলে গেল যে, এভারার্ডের কাছ থেকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি না পেলে আমি সেইদিনই দুপুরের গাড়িতে রওনা দিয়ে দিতাম।
ঘটনাটা ঘটতে বেশ রাত হল। আমার আশ্রয়দাতা আজ অন্যদিনের তুলনায় অনেক বেশি টেলিগ্রাম পেয়েছে। সেগুলো নিয়ে সে চলে গেল তার কাজের ঘরে। যখন বেরোল ততক্ষণে বাড়ির আর সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি শুনতে পেলাম সে রোজকার অভ্যাসমতো ঘুরে ঘুরে নীচের দরজাগুলো বন্ধ করছে। অবশেষে সে বিলিয়ার্ড রুমে এসে আমার সঙ্গে যোগ দিল, তার স্কুল দেহ ড্রেসিং গাউনে আবৃত, পায়ে একজোড়া টার্কিশ স্লিপার। আরাম কেদারায় বসে গেলাসে পানীয় ঢেলে সে নিজের সামনে টেনে নিল; লক্ষ করলাম তাতে জলের চেয়ে হুইস্কির মাত্রাই বেশি।
কী রাত রে বাবা! মন্তব্য করল এভারার্ড।
কথাটা ভুল বলেনি। সারা বাড়িটাকে ঘিরে ঝোড়ো বাতাস বইছে, তার শব্দ যেন প্রকৃতির আর্তনাদ। জানলাগুলো থরথর করে কাঁপছে, বাইরে অন্ধকারের ফলে ঘরের হলদে বাতিগুলো অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল বলে মনে হচ্ছে।
শুনি তোমার কাহিনী, বললেন আমার আশ্রয়দাতা। আমরা দুজনে এখন একা। এই দুর্যোগের রাতে কেউ আমাদের বিরক্ত করতে আসবে না। তুমি বলো, তারপর দেখি তোমর একটা হিল্লে করা যায় কিনা।
এইভাবে উৎসাহ দেবার ফলে আমি আদ্যোপান্ত বললাম আমার ব্যাপারটা। যেসব লোকের সঙ্গে আমার কারবার, আমার পাওনাদারেরা, আমার বাড়িওয়ালা, আমার চাকর-বাকর–কেউই সে বর্ণনা থেকে বাদ পড়ল না। সঙ্গে আমার নোটবুক ছিল, সব তথ্য গুছিয়ে নিয়ে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাবে আমার শোচনীয় অবস্থাটা তাকে বুঝিয়ে দিলাম। কিন্তু দেখে খারাপ লাগল যে, শ্রোতা আমার কথায় মনোযোগ দিচ্ছে না। যে দু-একটা মন্তব্য সে করছিল সেগুলো এতই মামুলি ও অপ্রত্যাশিত যে, আমার সন্দেহ হল সে আদৌ আমার কথা শুনছে না। মাঝে মাঝে হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে আমার কোনও উক্তির পুনরাবৃত্তি করতে বলে সে আগ্রহের একটা ভান করছিল বটে, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারছিলাম তার মন অন্যদিকে চলে গেছে। অবশেষে চেয়ার ছেড়ে উঠে চুরুটের অবশিষ্টাংশ ফায়ার প্লেসে ফেলে দিয়ে সে বলল, তোমায় বলি শোনো–হিসেব জিনিসটা কোনওদিন আমার মাথায় ঢোকে না। তুমি বরং পুরো ব্যাপারটা একটা কাগজে লিখে ফেললা, তারপর তোমার কত হলে চলে সেটাও লিখে দাও। চোখের সামনে জিনিসটা দেখতে পেলে আমার বুঝতে সুবিধা হবে।
প্রস্তাবটা শুনে আমার ভালই লাগল। আমি রাজি হয়ে গেলাম।
চলো এইবেলা শুয়ে পড়া যাক। ওই শোনো হলঘরের ঘড়িতে একটা বাজছে।
ঘড়ির ঘণ্টা ঝড়ের গোঙানি ছাপিয়ে শোনা গেল। বাতাসের শব্দ শুনে মনে হয়, যেন একটা উত্তাল নদী বয়ে চলেছে বাড়ির গা ঘেঁষে।
শোবার আগে বাঘটাকে একবার দেখে যেতে চাই, বলল এভারার্ড। ঝড় জিনিসটা ও ঠিক পছন্দ করে না। তুমি আসবে?
চলো।
চুপচাপ শব্দ না করে এসো। আর সবাই ঘুমোচ্ছে।
পারস্যের গালিচা বিছানো হলঘরে ল্যাম্প জ্বলছে; সে ঘর পেরিয়ে একটা দরজার মধ্যে দিয়ে গিয়ে ঢুকলাম প্যাসেজে। অন্ধকার প্যাসেজ, দেয়ালে একটি লণ্ঠন ঝুলছে। এভারার্ড সেটাকে নামিয়ে জ্বালিয়ে নিল। লোহার গরাদগুলো দেখা যাচ্ছে না, বুঝলাম বাঘ এখন খাঁচায় বন্দি।
এসো ভিতরে, বাঘের দরজা খুলে দিয়ে বলল এভারার্ড।
ঘরে ঢোকামাত্র একটা গর্জন শুনে বুঝলাম ঝড়ে বাঘের মেজাজ বেশ বিগড়ে দিয়েছে। ল্যাম্পের কম্পমান আলোয় দেখলাম বিশাল কৃষ্ণকায় জীবটিকে, খাঁচার এক কোণে খড়ের গাদার উপর বসে আছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। পিছনের সাদা দেয়ালে পড়েছে তার প্রকাণ্ড ছায়া। বাঘের লেজটা মাঝে মাঝে নড়ে উঠে মেঝের খড়গুলোকে ইতস্তত ছড়িয়ে দিচ্ছে।
বেচারি টমির মেজাজ তেমন সুবিধের নয়, হাতের ল্যাম্পটাকে এগিয়ে ধরে বলল এভারার্ড কিং। একটি আস্ত কেলে শয়তানের মতো দেখতে লাগে ওকে, তাই না? ওর জন্য কিছু খাদ্যের ব্যবস্থা না করলে ওর মেজাজ ভাল হবে না। দেখি ভাই, একটু ধরো তো লণ্ঠনটা।
আমি তার হাত থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। বাইরেই আছে ওর খাবার, বলল এভারার্ড, আমি এক মিনিটে ঘুরে আসছি। ও কথাটা বলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, আর সেই মুহূর্তে একটা ধাতব খুট শব্দের সঙ্গে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।
শব্দটা কয়েক মুহূর্তের জন্য আমার হৃৎস্পন্দন বন্ধ করে দিল। আমার সর্বাঙ্গে একটা আতঙ্কেব ঢেউ খেলে গেছে, একটা চরম বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কায় রক্ত হিম হয়ে গেছে। আমি দরজার উপর। লাফিয়ে পড়লাম–কিন্তু দেখলাম ঘরের ভিতর দিকে দরজার কোনও হাতল নেই।
দরজা খোলো! চেঁচিয়ে উঠলাম আমি, দরজা খোলো!
হল্লা কোরো না, প্যাসেজ থেকে উত্তর এল–তোমার কাছে আলো রয়েছে তো।
এভাবে একা বন্দি থাকতে চাই না আমি।
বটে? একটা বিশ্রী হসির সঙ্গে উত্তর এল। বেশিক্ষণ একা থাকতে হবে না তোমায়।
দরজা খোলো বলছি! আমি আবার চেঁচিয়ে উঠলাম। এ ধরনের রসিকতা আমি বরদাস্ত করতে পারি না।
এবারে একটা বিদ্রুপের হাসির সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের শব্দ ছাপিয়ে শুনলাম একটা যান্ত্রিক ঘড় ঘড় শব্দ। সর্বনাশ! হাতল ঘুরিয়ে লোহার ঝাঁঝরিটাকে টেনে বাইরে বার করে নিচ্ছে এভারার্ড কিং।
অর্থাৎ বাঘ আর খাঁচায় বন্দি থাকবে না।
লণ্ঠনের আলোতে দেখতে পাচ্ছি লোহার শিকগুলো ক্রমশ সামনে থেকে সরে যাচ্ছে। শিকওয়ালা দেয়াল যেখানে ঘরের দেয়ালের সঙ্গে গিয়ে ঠেকেছিল, সেখানে এর মধ্যেই প্রায় এক হাত ফাঁক দেখা দিয়েছে। মরিয়া হয়ে আমি শেষ শিকটা আঁকড়ে ধরে উলটো দিকে টানতে লাগলাম। রাগ ও আতঙ্কে তখন আমি দিশেহারা। দরজাটা দুদিক থেকে টানার ফলে মিনিটখানেক অনড় হয়ে রইল। বেশ বুঝতে পারছি ও সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে হাতলটা ঘোরাবার চেষ্টা করছে, এবং আর কিছুক্ষণের মধ্যে আমার শক্তি তার কাছে হার মানবে। এবার শিকটার সঙ্গে সঙ্গে আমিও হড়কাতে শুরু করেছি পাথরের মেঝের উপর দিয়ে। কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি এই পৈশাচিক মানুষটির হাতে যেন আমায় মরতে না হয়। অনেক অনুনয় করে তাকে বোঝালাম যে, আমার সঙ্গে তার রক্তের সম্পর্ক। আমি তার অতিথি। আমি তার কী ক্ষতি করেছি যে, সে আমার সঙ্গে এমন আচরণ করছে!–কিন্তু জবাবে সে আরও বলপ্রয়োগ করে চলেছে হাতলের উপর, এবং একটি একটি করে লোহার শিক বেরিয়ে চলেছে ঘরের বাইরে। টানের চোটে আমিও এগিয়ে চলেছি খাঁচার সামনে দিয়ে।
অবশেষে আমার কবজি যখন যন্ত্রণায় অসাড়, আমার আঙুল ক্ষতবিক্ষত, তখন নিরুপায় হয়ে হাল ছাড়তে হল। একটা ঘটাং শব্দ করে খাঁচার দেওয়ালটা পুরো সরে গেল, আর তারপর শুনলাম টার্কিশ চটি পরা পায়ের শব্দ মিলিয়ে গিয়ে প্যাসেজের শেষ প্রান্তের দরজাটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। তারপর আর শব্দ নেই।
এতক্ষণ জানোয়ারটা অনড় ভাবেই বসে ছিল খাঁচার এক কোণে। তার লেজ আর নড়ছে না। তার সামনে দিয়ে একটা মানুষকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে–এ দৃশ্য নিশ্চয়ই তার ভারী অদ্ভুত লেগেছিল। তার বিশাল চোখ দুটি এখন আমার দিকে চাওয়া। শিকটা ধরার সময় লণ্ঠনটা মেঝেতে নামিয়ে রেখেছিলাম। মনে হল সেটা হাতে থাকলে তার আলোটা হয়তো আত্মরক্ষায় কিছুটা সাহায্য করবে; কিন্তু সেটা তুলতে যেই হাত নামিয়েছি অমনই বাঘটা একটা হুঙ্কার দিয়ে উঠল। আমি তৎক্ষণাৎ আতঙ্কে পাথর। বাঘের থেকে আমার দূরত্ব এখন মাত্র দশ ফুট। তার চোখ দুটো আগুনের ভাঁটার মতো জ্বলছে। অদ্ভুত সে চাহনি; মনের গভীরে ত্রাসের সঞ্চার করলেও চোখ ফেরানো যায় না। চরম সংকটের মুহূর্তে প্রকৃতির আশ্চর্য খেয়ালে মনে হয় জ্বলন্ত গোলক দুটি যেন একবার আয়তনে বাড়ছে, একবার কমছে। আবার মনে হয় যে, অন্ধকারে দুটি উজ্জ্বল বিন্দু ক্রমে বড় হতে হতে ঘরের ওই বিশেষ অংশটিতে একটা ভৌতিক আভা ছড়িয়ে দিচ্ছে। আর তারপরেই দেখি আলো নেই।
অর্থাৎ জানোয়ার চোখ বন্ধ করেছে। মানুষের অপলক দৃষ্টিতে এক অমোঘ শক্তি আছে, এমন একটা প্রচলিত ধারণায় কোনও সত্য আছে কিনা জানি না; হয়তো বা জানোয়ারটার মধ্যে একটা তার ভাব এসেছিল। মোট কথা, আক্রমণের কোনও চেষ্টার বদলে সেটা দিব্যি পায়ের উপর মাথা রেখে ঘুমোচ্ছ বলেই মনে হয়। পাছে তার মধ্যে আবার হিংস্রভাব জেগে ওঠে, তাই আমিও সম্পূর্ণ অনড় হয়ে রইলাম। ওই ভয়ংকর চোখ দুটো আমার চোখের সামনে না থাকায় এখন তবু মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবতে পারছি। এই পৈশাচিক জানোয়ারের সঙ্গে সারারাত সহবাস করতে হবে আমাকে। আমার নিজের মন বলছে, এবং যার জন্য আমার এই দশা তার কথাতেও বুঝেছি যে, এই জানোয়ার। তার মনিবের মতোই মারাত্মক। কাল সকাল পর্যন্ত একে ঠেকিয়ে রাখব কী করে? দরজা তো খুলবেই না, আর ওই শিকওয়ালা খুপচি জানলাও আমার কোনও কাজে আসবে না। আমাকে বাঁচাও বলে তারস্বরে চেঁচিয়ে কোনও লাভ নেই, কারণ আমি এখন যে অংশটাতে রয়েছি সেটা বাড়ির বাইরে; সেই বাড়ি আর ব্যাঘ্রাবাসের মধ্যে যে প্যাসেজটা রয়েছে সেটা প্রায় একশো ফুট লম্বা। তা ছাড়া এই ঝড়বাদলের শব্দের মধ্যে আমার চিৎকার শুনবে কে? একমাত্র ভরসা আমার সাহস ও উপস্থিতবুদ্ধি।
ঠিক এই মুহূর্তে আমার অসহায়ভাব দ্বিগুণ বেড়ে গেল লণ্ঠনের দিকে চোখ পড়াতে। বাতির যে এখন শেষ অবস্থা সেটা শিখার অস্থিরতা থেকেই বোঝা যায়। এর আয়ু দশ মিনিট। যা করার এর মধ্যেই, কারণ অন্ধকারে ওই জানোয়ারের সঙ্গে একা পড়লে তখন আর সুস্থমস্তিষ্কে কিছু করার অবস্থা থাকবে না। কথাটা ভাবতেই আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অসাড় হয়ে এল। দিশেহারা ভাবে এদিক-ওদিক চাইতে একটা জিনিসের উপর চোখ পড়াতে একটা ক্ষীণ আশার উদ্রেক হল। এতে সংকট থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি না পেলেও, অন্তত সাময়িক নিরাপত্তার একটা সম্ভাবনা আছে।
আগেই বলেছি যে, খাঁচার দুটো অংশ ছিল–একটা ছাত ও একটা সামনের দেয়াল। দেয়ালটা বাইরে বার করে নিলেও, ছাতের অংশটা ভিতরেই থেকে যায়। এই ছাতেও কয়েক ইঞ্চি অন্তর অন্তর একটা করে লোহার শিক, আর শিকের মধ্যে ফাঁকগুলো ভরা লোহার জাল দিয়ে। সেই আচ্ছাদনের নীচে খাঁচার এক কোনায় এখন বসে আছে বাঘটা। খাঁচার ছাত আর ঘরের সিলিং-এর মধ্যে হাত দুয়েকের ব্যবধান। যদি কোনওরকমে ওই ছাতের উপর উঠতে পারি, তা হলে অন্তত পিছন থেকে, মাথার দিক থেকে, আর দুপাশ থেকে আমি নিরাপদ। খোলা থাকবে শুধু সামনের দিকটা। সেদিক থেকে বাঘ আমায় আক্রমণ করতে পারে ঠিকই, কিন্তু তা হলেও বলব যে, বাঘ যদি হঠাৎ ঘরে পায়চারি শুরু করে তা হলে আমাকে তার সামনে পড়তে হবে না। আমার নাগাল যদি তাকে পেতে হয় তা হলে কিছুটা কসরত করতে হবে। যা করার এইবেলা, কারণ বাতি নিভে গেলে কাজটা আমার। পক্ষে অনেক বেশি কঠিন হয়ে পড়বে।
যা থাকে কপালে করে, এক লাফে ছাউনির পাশটা দুহাতে খামচে ধরে দেহটাকে কোনওমতে। উপরে নিয়ে গিয়ে ফেললাম। আমার মুখ তখন দুই শিকের মাঝখানে জালের উপর; দেখতে পাচ্ছি বাঘের মুখ হাঁ, আর তার ভয়ংকর চোখ দুটো চেয়ে আছে সটান আমার দিকে, তার নিশ্বাসের বোঁটকা গন্ধে আমার নাক জ্বলছে।
জানোয়ারের ভাব দেখে কিন্তু মনে হল, রাগের চেয়ে তার কৌতূহলটাই যেন বেশি। এবারে সে তার দেহের মাংসপেশিতে ঢেউ খেলিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পিছনের দুপায়ে ভর করে একটা থাবা পিছনের দেয়ালে রেখে অন্যটা দিয়ে খাঁচার ছাতের জালের উপর দিয়ে একটা লম্বা আঁচড় টানল। তার ফলে তার নখ আমার পাতলুন ভেদ করে আমার হাঁটুতে একটা গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করল। এটাকে আক্রমণ বলা চলে না, বরং আক্রমণের মহড়া মাত্র, কারণ আমার আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে সে থাবা নামিয়ে নিয়ে এক লাফে খাঁচা থেকে বেরিয়ে সারা ঘর জুড়ে দ্রুত পায়চারি শুরু করে দিল। তারই ফাঁকে ফাঁকে তার দৃষ্টি বারবার চলে আসছে আমার দিকে। আমি দেহ সঙ্কুচিত করে নিজেকে একেবারে দেয়ালের সঙ্গে সিটিয়ে দিলাম। যত পিছিয়ে থাকব, ততই তারপক্ষে আমার নাগাল পাওয়া কঠিন হবে।
বাঘের উত্তেজনা যেন ক্রমেই বাড়ছে, হাঁটার গতিও বাড়ছে সেইসঙ্গে, তার অস্থির পদক্ষেপ বারবার তাকে নিয়ে আসছে আমার লৌহাসনের ঠিক নীচে। আশ্চর্য এই ছায়াসদৃশ বিশাল শ্বাপদের নিঃশব্দ গতি! এদিকে লণ্ঠনের আলো এতই মৃদু যে, তাতে বাঘকে প্রায় দেখাই যায় না। অবশেষে একবার দপ করে জ্বলে উঠে লণ্ঠনটা নিভেই গেল। সূচিভেদ্য অন্ধকারে এখন শুধু আমি আর বাঘ।
বিপদের সামনে পড়ে যদি বুঝতে পারি যে, আমার যথাসাধ্য আমি করেছি, তা হলে শুধু পরিণতির অপেক্ষা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। বর্তমান ক্ষেত্রে আমি যেখানে যে অবস্থায় আছি, সেটাই হল আমার পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। আমি সেইভাবেই হাত-পা গুটিয়ে প্রায় দমবন্ধ করে পড়ে রইলাম। আশা আছে আমার অস্তিত্ব জানান না দিলে বাঘ হয়তো আমার কথা ভুলে যাবে। আন্দাজে মনে হয় দুটো বাজতে চলল। ভোর হবে চারটায়। দিনের আলোর জন্য অপেক্ষা করতে হবে আরও দু ঘণ্টা।
বাইরে ঝড় চলেছে পুরোমাত্রায়। বৃষ্টির জল এসে আছড়ে পড়ছে জানলার গায়ে। ঘরের ভিতরে রাক্ত জান্তব গন্ধে আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত। বাঘ এখন আমার কাছে অদৃশ্য। তার কোনও শব্দ আসছে না আমার কানে। আমি বাঘের চিন্তা মন থেকে দূর করে অন্য কথা ভাবার চেষ্টা করলাম। একটি চিন্তাই স্থান পেল মনে; সেটা হল আমার খুড়তুতো ভাইটির শয়তানি, তার চরম বিশ্বাসঘাতকতা, আর আমার প্রতি তার গভীর বিদ্বেষের ভাব। ওই গালভরা হাসির পিছনে লুকিয়ে আছে এক নৃশংস খুনি। যতই ভাবলাম, ততই তার পরিকল্পনার চাতুরিটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে এল। সকলের সঙ্গে সেও চলে গিয়েছিল শুতে, তারপর গোপনে ফিরে এসে আমাকে তার বাঘের ঘরে নিয়ে গিয়ে বন্দি করে রেখে চলে যায়। অত্যন্ত সহজেই সে ঘটনাটা বুঝিয়ে দেবে আর পাঁচজনকে। বিলিয়ার্ড রুমে বসে চুরুটটা শেষ করে তবে আমি উঠব; সে আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গুডনাইট করে চলে যায়। আমি নিজের খেয়ালবশত দিনের শেষে একবার বাঘটা দেখতে যাই, খাঁচা খোলা আছে না জেনে ঘরে ঢুকি, আর তার ফলেই ফাঁদে পড়ি। এর জন্য তাকে দায়ী করবে কে? আর যদি বা তার উপর সন্দেহ হয়–প্রমাণ তো নেই!
দু ঘণ্টা সময় যেন কাটতেই চায় না। একবার একটা খস্ খস্ শব্দে বুঝলাম বাঘ তার নিজের গায়ের লোম চাটছে। বার কয়েক একজোড়া সবুজ আলো দেখে মনে হল সে আমার দিকে চাইছে, কিন্তু তাও বেশিক্ষণের জন্য নয়। ক্রমে একটা বিশ্বাস দানা বাঁধতে লাগল যে, সে হয়তো আমার অস্তিত্ব ভুলে গেছে; কিংবা আমাকে অগ্রাহ্য করা সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অবশেষে জানলা দিয়ে একটা ক্ষীণ আলো ঘরে প্রবেশ করল। প্রথমে দেখলাম দেয়ালের গায়ে এক জোড়া ধূসর চতুষ্কোণ; তারপর সে-দুটো ক্রমে সাদায় পরিণত হল; তারপর আমার সহবাসিন্দাটি প্রতীয়মান হবার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম বাঘও আমার দিকে চেয়ে আছে।
দৃষ্টি বিনিময়ের পরমুহূর্তেই বুঝতে পারলাম যে শেষ দেখার সময় যা মনে হয়েছিল, বাঘের। মেজাজ তার চেয়ে শতগুণে বেশি ভয়ংকর। ভোরের শীত তার মোটেই পছন্দ হচ্ছে না; তার উপর সে হয়তো ক্ষুধার্ত। ঘরের ওপাশটায় অনবরত গর্জনের সঙ্গে সে দ্রুত পায়চারি করছে। পাথরের মেঝের উপর বার বার আছড়ে পড়ছে তার লেজ। কোণ অবধি গিয়ে উলটো মুখে ঘোরার সময় তার নির্মম দৃষ্টি চলে আসছে আমার দিকে। বুঝতে পারলাম আমাকে সে আস্ত রাখবে না। কিন্তু এইরকম হতাশার মুহূর্তেও এই ভয়াল পশুর গতিবিধির আশ্চর্য সাবলীলতা, তার পেশল দেহের ভাস্কর্যসুলভ সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ না করে পারল না। এদিকে চাপা গর্জন ক্রমে অসহিষ্ণু হুঙ্কারে পরিণত হচ্ছে, বেশ বুঝতে পারছি আমার অন্তিম সময় উপস্থিত।
এইভাবেই কি শেষে মরতে হবে–এই লোহার গরাদের উপর শুয়ে শীতে কম্পমান অবস্থায়? আমার অন্তরাত্মাকে এই শোচনীয় অবস্থার উর্ধ্বে উত্তরণের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে, একজন মুমূর্ষ ব্যক্তির চিন্তায় যে স্বচ্ছতা আসে তার সাহায্যে ভাবতে চেষ্টা করলাম আত্মরক্ষার কোনও উপায় আছে কিনা। ভেবে একটা জিনিসই মনে হল যে, খাঁচার দেয়ালটা কোনওরকমে বাইরে থেকে আবার ভিতরে এনে বসিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে সেটাই হবে বাঁচার একমাত্র পথ। ওটাকে কি টেনে আনা যায়? এদিকে এও বুঝতে পারছি যে, অঙ্গ সঞ্চালনার সামান্য ইঙ্গিতেই বাঘ হয়তো আমাকে আক্রমণ করে বসবে।
অত্যন্ত সন্তর্পণে ডান হাতটা বাড়িয়ে খাঁচার দেয়ালের যে দিকটা ঘরের মধ্যে রয়ে গিয়েছিল সেটাকে ধরলাম। আশ্চর্য এই যে, একটা টান দিতেই সেটা খানিকটা এগিয়ে এল আমার দিকে। কিন্তু আমি যে অস্বস্তিকর অবস্থায় রয়েছি তাতে খুব বেশি জোর দিয়ে টানা সম্ভব নয়। আরেকবার টান দিতে ইঞ্চি তিনেক ঢুকে এল দেয়ালটা। এবার বুঝলাম দেয়ালের তলায় চাকা লাগানো রয়েছে। আরেকবার দিলাম টান–সেই মুহূর্তেই বাঘটা দিল লাফ।
ব্যাপারটা এত আচমকা ঘটল যে, আমি টেরই পাইনি। শুধু কানে এল একটা হুঙ্কার, আর সেইসঙ্গে আমার চোখের সামনে দেখলাম এক জোড়া জ্বলন্ত হলুদ চোখ ও মিশকালো মুখে দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরোনো একটা ললকে লাল জিভ। বাঘ লাফিয়ে পড়ার ফলে আমার লৌহাসন থরথর করে কেঁপে উঠেছে–মনে হয় এই বুঝি সবসুদ্ধ ভেঙে পড়ল। বাঘটা কিছুক্ষণ সেই অবস্থায় রইল, তার মাথা ও সামনের থাবা আমার থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে, আর পিছনের থাবা খাঁচার দেয়ালে একটা অবলম্বন খোঁজার চেষ্টায় অস্থির। কিন্তু লাফটা ঠিক জুতসই হয়নি। বাঘ সেই অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকতে পারল না। প্রচণ্ড রাগে দাঁত খিঁচিয়ে জালে আঁচড় দিতে দিতে সে সশব্দে লাফিয়ে নেমে পড়ল মেঝেতে। কিন্তু তার পরেই আবার আমার দিকে ফিরে দ্বিতীয়বার লক্ষ্যের জন্য প্রস্তুত হল।
আমি জানি আমার চরম পরীক্ষার সময় উপস্থিত। বাঘ একবার ঠেকে শিখেছে, দ্বিতীয়বার আর সে ভুল করবে না। আমার বাঁচতে হলে যা করার তা করতে হবে এই মুহূর্তে। এক ঝলকে পন্থা স্থির করে নিলাম। চোখের নিমেষে আমার কোটটা খুলে নিয়ে সেটাকে জানোয়ারটার মাথার উপর ছুঁড়ে ফেললাম, আর প্রায় একই মুহূর্তে এক লাফে খাঁচার হাত থেকে লাফিয়ে নেমে দেয়ালের শিকটা ধরে প্রাণপণে দিলাম টান।
যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক সহজেই দেয়ালটা ঘরের মধ্যে চলে এল। আমি যত দ্রুত সম্ভব সেটাকে খাঁচার অপর প্রান্তে টেনে নিয়ে গেলাম, কিন্তু সেইভাবে টানার ফলে আমি নিজে রয়ে গেলাম খাঁচার বাইরে। ভিতরে থাকলে হয়তো আমি রেহাই পেতে পারতাম, কিন্তু সেটা করার চেষ্টায় আমাকে যে কয়েক মুহূর্ত থামতে হল তাতে বাঘটা তার মাথা থেকে কোটটা ফেলে দিয়ে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আমি খাঁচার সামনেটা বন্ধ করে ভিতরে ঢুকে এসেছি, কিন্তু তার আগে বাঘটা তার থাবার এক চাপড়ে আমার পায়ের ডিমের বেশ খানিকটা অংশ তুলে নিয়েছে র্যাঁদা দিয়ে চাঁছা কাঠের মতো করে। পরমুহূর্তেই যন্ত্রণায় প্রায় বেহুঁশ হয়ে আমি খাঁচার ভিতরে খড় বিছানো মেঝেতে লুটিয়ে পড়লাম। আমার সামনে খাঁচার গরাদ, আর তার উপর নিষ্ফল ক্রোধে বারবার আঘাত করছে ব্রেজিলের বাঘ। অর্ধমৃত অবস্থায় আমার মন থেকে আতঙ্কের ভাব দূর হয়ে গেছে, আমি সামনের দিকে চেয়ে দেখছি বাঘ তার কালো বুকটা গরাদের উপর রেখে তার থাবা দিয়ে আমার নাগাল পাবার চেষ্টা করছে, ঠিক যেমন কলে ধরা-পড়া ইঁদুরের নাগাল পেতে চেষ্টা করে বেড়াল। আমার জামায় এসে ঠেকছে তার নখগুলো, কিন্তু গায়ের চামড়া পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে না। শুনেছিলাম বাঘ বা ওই জাতীয় জানোয়ারের দ্বারা জখম হলে মানুষের মধ্যে কেমন যেন একটা অসাড় ভাব আসে। সেটা এখন দিব্যি অনুভব করছি। আমি যেন আর আমি নই, কোনও এক তৃতীয় ব্যক্তি যেন কৌতূহলের সঙ্গে দেখে চলেছে বাঘটা তার চেষ্টায় কৃতকার্য হয় কিনা। তারপর ক্রমে আমার চেতনা লোপ পেয়ে আমি যেন এক দুঃস্বপ্নের জগতে চলে গেলাম, যেখানে আমার চোখের সামনে রয়েছে কেবল বাঘের সেই কালো মুখ আর তার থেকে বেরিয়ে আসা লকলকে লাল জিভ। সবশেষে আমার লাঞ্ছনার শেষ হল এক মোহাচ্ছন্ন প্রলাপের অবস্থায়।
এখন ভাবলে মনে হয় আমি অন্তত ঘণ্টা দুই এইভাবে অজ্ঞান হয়ে ছিলাম। জ্ঞান হল সেই তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দে, যাতে আমার বিপদের সূত্রপাত। খাঁচার দেয়াল আবার বাইরে বেরিয়ে তার খাপে বসল। তারপর সম্পূর্ণ জ্ঞান হবার আগেই দেখলাম আমার ভাইয়ের সেই গোল হাসিভরা মুখ খোলা দরজা দিয়ে ঘরের ভিতর উঁকি মারছে। সে যা দেখল তাতে সে নিশ্চয়ই অবাক হয়েছিল। বাঘ বসে আছে খাঁচার বাইরে ঘরের মেঝেতে, আর আমি ছিন্নভিন্ন পাতলুনে কোটবিহীন অবস্থায় রক্তাপ্লুত দেহে পড়ে আছি খাঁচার ভিতর। সকালের রোদ পড়া মুখে তার চরম বিস্ময়ের ভাবটা এখনও দেখতে পাচ্ছি চোখের সামনে। সে একবার দেখল আমার দিকে, তারপর আবার। তারপর ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে খাঁচার দিকে এগিয়ে এসে আবার দেখল আমি সত্যি মরে গেছি কিনা।
ঘটনার সঠিক বর্ণনা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তখন যা অবস্থা তাতে সবকিছু সম্যক অনুধাবন করার সামর্থ্য ছিল না আমার। শুধু এইটুকু দেখলাম যে, তার দৃষ্টিটা হঠাৎ আমার দিক থেকে সরে গিয়ে গেল বাঘের দিকে।
শাবাশ, টমি, শাবাশ! উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল এভারার্ড কিং।
তারপর সে হঠাৎ খাঁচার দিকে পিছিয়ে এসে চেঁচিয়ে উঠল–সরে যাও বলছি, সরে যাও! মুখ জানোয়ার–তোমার মনিবকে চেনো না তুমি?
এই মুহ্যমান অবস্থাতেও কিং-এর একটা উক্তি আমার হঠাৎ মনে পড়ল। মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে নিরীহ জানোয়ারও রাক্ষসে পরিণত হয়। এই পরিণতির জন্য আমার রক্তই দায়ী, কিন্তু তার মাশুল দিতে হবে আমাকে নয়, আমার এই ভাইটিকে।
সরে যাও বলছি! চিৎকার করে উঠল এভারার্ড কিং। সরে যাও শয়তান! বল্ডউইন! বল্ডউইন!–ওরে বাবা রে!…..
তারপর দেখলাম সে মাটিতে পড়ল। পড়ল, উঠল, আবার পড়ল, আর সেইসঙ্গে এক রক্ত-হিম করা শব্দ–যেন কাপড় ছেঁড়া হচ্ছে ফালা ফালা করে। আর্তনাদের শব্দ ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এসে শেষে যে শব্দটা রইল সেটা মানুষের নয়, জানোয়ারের! আর তারপর, যখন ভাবছি সে মরে গেছে, তখন এক বিভীষিকাময় মুহূর্তে দেখলাম একটি অর্ধমৃত, প্রায়ান্ধ, রক্তাক্ত মানুষ পাগলের মতো ঘরের চারিদিকে ছুটে বেড়াচ্ছে। তারপর আমিও সংজ্ঞা হারালাম।
বেশ কয়েক মাস লেগেছিল আমার সুস্থ হয়ে উঠতে। সম্পূর্ণ সুস্থ হইনি, কারণ সেই ব্রেজিলীয় শার্দুলের সঙ্গে রাত্রিযাপনের চিহ্নস্বরূপ আজও আমাকে একটি লাঠি হাতে চলতে হয়। বল্ডউইন, বাঘের পরিচারক এবং অন্যান্য চাকরবাকর যখন এভারার্ডের আর্তনাদ শুনে বাঘের ঘরে এসে খাঁচার মধ্যে আমায় এবং বাঘের কবলে তাদের মনিবের অবিশিষ্টাংশ দেখতে পায়, তখন কেমন করে এ ঘটনা ঘটল সেটা তারা অনুমান করতে পারেনি। তপ্ত লোহার শিকের সাহায্যে বাঘকে কোণঠাসা করে দরজার ফাঁক দিয়ে গুলি করে তাকে মেরে আমাকে খাঁচার ভিতর থেকে উদ্ধার করা হয়। সেখান থেকে শোবার ঘরে নিয়ে যাওয়া হয় আমাকে। তারপর বেশ কয়েক সপ্তাহ আমার শত্রুর বাড়িতে থেকেই মৃত্যুর সঙ্গে লড়তে হয়েছিল আমাকে। ক্লিপটন থেকে এসেছিলেন এক সার্জন, আর লন্ডন থেকে নার্স। এক মাস পরে আমাকে পৌঁছে দেওয়া হয় স্টেশনে, আর সেখান থেকে আমি চলে আসি আমার বাসস্থান গ্রোভনর ম্যানসনসে।
আমার অসুখের সময়ের একটা ঘটনা আমার মনে আছে। অত্যন্ত স্পষ্ট হওয়াতে এই স্মৃতিটাকে আমার স্বরবিকারজনিত দুঃস্বপ্নের অঙ্গ বলে মনে হয় না। এক রাত্রেনার্স তখন আমার ঘরে নেই–দরজা খুলে প্রবেশ করলেন এক দীঘাঙ্গিনী, তাঁর পরনে বিধবার কালো পোশাক। তিনি কাছে এসে আমার উপর ঝুঁকে পড়াতে দেখলাম এভারার্ড যে ব্রেজিলীয় মহিলাটি বিবাহ করেছিল, ইনি তিনিই। তাঁর চাহনিতে যে করুণা ও সহানুভূতি দেখলাম, তেমন আর কোনওদিন দেখিনি।
আপনার জ্ঞান আছে? জিজ্ঞেস করলেন মহিলা।
আমি তখন খুবই দুর্বল, তাই মুখে কিছু না বলে মাথা নেড়ে হ্যাঁ জানালাম।
আমি এইটুকু বলতে এসেছি যে, আপনার এই দুর্দশার জন্য আপনিই দায়ী। আমি তো চেষ্টার কোনও ত্রুটি করনি। প্রথম থেকেই চেয়েছিলাম যাতে আপনি না থাকেন। আপনি যাতে তাঁর কবলে না পড়েন তার জন্য আমার স্বামীকে বঞ্চনা করে যতটা করা সম্ভব সবই করেছিলাম আমি।
আমি জানতাম সে আপনাকে কেন ডেকে এনেছিল। আমি জানতাম সে আর কোনওদিন আপনাকে ফিরে যেতে দেবে না। আমি যত ভাল করে চিনতাম তাকে, তেমন তো আর কেউ চিনত না! আমি নিজে যে ভূক্তভোগী! সে কথা তো আর আপনাকে বলা যায় না। কিন্তু আপনার যাতে মঙ্গল হয় তার চেষ্টার ত্রুটি করিনি আমি। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, আপনি আমার বন্ধুর কাজ করেছেন। আমি ভাবতাম আমার মৃত্যু না হলে আমার মুক্তি নেই, কিন্তু আপনি আমার মুক্তি দিয়েছেন তাঁর কবল থেকে। আপনার এত কষ্টভোগ করতে হল বলে আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি তো বলেইছিলাম–আপনি মূর্খ, এবং মূর্খের মতোই কাজ করেছিলেন আপনি।
কথাটা বলে চলে গেলেন সেই আশ্চর্য মহিলা, যাঁকে আর কোনওদিন দেখিনি আমি। স্বামীর সম্পত্তি থেকে তাঁর যা প্রাপ্য তাই নিয়ে তিনি দেশে ফিরে গিয়েছিলেন, এবং পরে নাকি সন্ন্যাসিনী হয়ে গিয়েছিলেন।
লন্ডনে ফেরার বেশ কিছুদিন পরে ডাক্তার আমাকে জানালেন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ, এবং আবার কাজ শুরু করতে পারি। কথাটা শুনে আমার মনটা যে খুব প্রসন্ন হল তা নয়, কারণ কাজ মানেই পাওনাদারের স্রোত রোধ করার চেষ্টা। আসল খবরটা প্রথম দিল আমার উকিল সামান্স।
আপনি আবার সুস্থ হয়ে উঠেছেন এটা খুবই আনন্দের কথা, বলল সামারস। আপনাকে অভিনন্দন জানানোর জন্য অপেক্ষা করছিলাম আমি।
অভিনন্দন? তুমি কী বলছ সামারস! মশকরা করার সময় নয় এটা।
যা বলছি ঠিকই বলছি, বলল সামারস। গত দেড় মাস হল আপনি লর্ড সাদারটন হয়েছেন। পাছে অসুস্থ অবস্থায় খবরটা পেলে আপনার রোগমুক্তিতে ব্যাঘাত ঘটে, তাই এতদিন বলিনি।
লর্ড সাদারটন! ইংল্যান্ডের অন্যতম সবচেয়ে বিত্তবান অভিজাত বংশের প্রতিভূ। আমি আমার কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তারপর মনে পড়ল যে, অনেকটা সময় তো পেরিয়ে গেছে এর মধ্যে, আর আমি তো এই সময়টা ছিলাম শয্যাশায়ী। বললাম, তাহলে লর্ড সাদারটন মারা গেছেন আমি অসুস্থ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই?
ঠিক সেই একই দিনে, আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে বলল সামারস। সে বুদ্ধিমান লোক, সে কি আর অনুমান করতে পারেনি আমার দুর্দশার কারণটা? কিন্তু আমি তাকে কিছু বললাম না। তার কাছে আগ বাড়িয়ে পারিবারিক কুৎসা রটাতে যাব কেন?
হুঁ, ব্যাপারটা খুবই আশ্চর্য, আমার দিকে সেই একই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সে বলল। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, আপনার অবর্তমানে এই এভারার্ড কিংই পেতেন ওই খেতাব। তিনি না হয়ে আপনি যদি ওই বাঘের কবলে পড়তেন তা হলে উনিই হতেন লর্ড সাদারটন।
তা তো বটেই, বললাম আমি।
আর ভদ্রলোক এ ব্যাপারে খুবই আগ্রহী ছিলেন, বলল সামার। আমি জানি লর্ড সাদারটনের চাকরের সঙ্গে ওঁর যোগাযোগ ছিল, আর সেই চাকর ঘন ঘন টেলিগ্রাম করে কিংকে জানাত তার মনিবের অবস্থা। সেই সময়টা আপনি কিং-এর বাড়িতে। আপনি উত্তরাধিকারী, অথচ বারবার সে খোঁজ নিচ্ছে লর্ড সাদারটনের ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত নয় কি?
নিঃসন্দেহে, বললাম আমি। আর শোনো, সামান্স–এবার তো কাজকর্ম শুরু করে দিতে হয়। দাও তো দেখি আমার বিলগুলো আর আমার নতুন চেক বইটা!
দি ব্রাজিলিয়ান ক্যাট
সন্দেশ, শারদীয়া ১৩৮৯
-জন গহ্বরের বিভীষিকা
১৯০৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি সাউথ কেনসিংটনের ৩৬ নং আপার কভেন্ট্রি ফ্ল্যাটে যক্ষ্মা রোগে ডাঃ জেস হার্ডকাসূলের মৃত্যুর পর, তাঁর কাগজপত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত কাহিনীটি পাওয়া যায়। যাঁরা হার্ডকাকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন, তাঁরা একাহিনী সম্পর্কে কোনও মন্তব্য না করলেও, অন্তত এটুকু একবাক্যে স্বীকার করেন যে, হার্ডকাল একজন সুস্থমস্তিষ্ক বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন; তাঁর পক্ষে নিছক মনগড়া কতগুলো আজগুবি ঘটনাকে বাস্তব বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা খুবই অস্বাভাবিক ছিল।
লেখাটা পাওয়া যায় একটা খামের মধ্যে। তার শিরোনামায় বলা হয়েছে–গত চৈত্র মাসে উত্তর-পশ্চিম ডার্বিশায়ারে অ্যালারটনদের ফার্মের নিকটবর্তী স্থানের একটি ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। বন্ধ খামের পিছনে ছিল পেনসিলে লেখা এই চিঠি–
প্রিয় সিটন,
শুনে আঘাত পাবে কিনা জানি না আমার কাহিনী তুমি অবিশ্বাস করার ফলে আমি সে বিষয়ে আজ পর্যন্ত আর কারুর কাছে কোনও উল্লেখ করিনি। হয়তো বা আমার মৃত্যুর পর শেষ পর্যন্ত কোনও অপরিচিত ব্যক্তি এই কাহিনীর উপযুক্ত মর্যাদা দেবে, যে মর্যাদা থেকে আমার বন্ধু আমায় বঞ্চিত করেছিল।
এই সিটন ব্যক্তিটি যে কে, সেটা অনুসন্ধান করেও জানা যায়নি। ইতিমধ্যে, মৃত ব্যক্তি যে অ্যালারটনদের ফার্মে সত্যিই গিয়েছিলেন, এবং তাঁর থাকাকালীন যে ভয়াবহ ঘটনা সেখানে ঘটেছিল, এবং সেই ঘটনার যে আনুমানিক কারণ তিনি তাঁর লেখায় ব্যক্ত করেছেন, সে সবই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই সামান্য ভূমিকাটুকু দিয়ে, ডায়েরির আকারে বর্ণিত হার্ভকালের বিচিত্র কাহিনীটি অবিক ভাবে নীচে উদ্ধৃত করা হল :
১৭ এপ্রিল
এই জায়গাটির জলবায়ুর গুণ এর মধ্যেই বেশ অনুভব করছি। অ্যালারটনদের ফার্মের উচ্চতা ১৪২০ ফুট, সুতরাং এখানকার আবহাওয়া স্বাস্থ্যকর হওয়াই স্বাভাবিক। সকালে সেই কাশির ভাবটা ছাড়া অন্য কোনও অসোয়াস্তি নেই, আর টাটকা দুধ ও মাংস খাওয়ার ফলে ওজন বৃদ্ধির সম্ভাবনাও সুস্পষ্ট। স্যান্ডারসন আমার অবস্থা শুনলে খুশিই হবে।
অ্যালারটন ভগিনীদ্বয় দুজনেই বেশ মজার ও অমায়িক প্রকৃতির মহিলা। দুজনেই অবিবাহিতা। ফলে, স্বামী ও সন্তানের অভাবে দুজনেরই স্নেহের শেষ কণাটুকু বর্ষিত হচ্ছে এই রুগণ ব্যক্তিটির উপর। অবিবাহিতা মহিলারা সংসারে অপ্রয়োজনীয়, এ ধরনের একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে বলে জানি; কিন্তু আমি ভাবি, এদের অভাবে আমাদের মতো অকৃতদার অপ্রয়োজনীয় পুরুষদের দশা কী। হত। স্যান্ডারসন যে কেন আমায় এখানে আসতে বলেছিল, তার কারণটা দুই বোনের কথাবাতায় প্রকাশ পেয়ে গেছে। আসলে, আজ অধ্যাপকের আসনে প্রতিষ্ঠিত হলেও, স্যান্ডারসনের জীবনের শুরু হয়েছিল এই গ্রাম্য পরিবেশেই। হয়তো ছেলেবেলায় সে এই খামারের আশেপাশে কাক-চড়ই তাড়িয়ে বেড়িয়েছে।
অসমতল উপত্যকার মাঝখানে অবস্থিত এই গ্রামটি ভারী নির্জন, নিস্তব্ধ। এর পথঘাটগুলি ছবির মতো সুন্দর। দুপাশে খাড়াই উঠে গেছে লাইমস্টোনের পাহাড়। এই পাহাড়ের পাথর এতই নরম যে, হাতের চাপে আলগা হয়ে খসে আসে। এখানকার জমির ভিতরটা মনে হল ফাঁপা। একটা অতিকায় হাতুড়ি নিয়ে যদি এই জমির উপর ঘা দেওয়া হয়, তা হলে বোধহয় তা থেকে গুরুগম্ভীর জয়টাকের মতো শব্দ বেরোবে। তেমন জোরে ঘা দিলে হয়তো বা জমি ধসে গিয়ে ভূগর্ভস্থিত কোনও বিশাল সমুদ্রের সন্ধান মিলবে। এসব পাহাড়ের ভিতর জলাশয়ের অস্তিত্ব মোটেই অসম্ভব নয় কারণ বাইরে থেকে পরিষ্কার দেখা যায়, অজস্র জলধারা পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে নানান। ফাটলের মধ্য দিয়ে আবার পাহাড়েরই ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে। এমন বড় বড় ফাটলও কিছু রয়েছে, যার মধ্য দিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হলে মনে হয় যেন আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গপথ দিয়ে তারা সোজা একেবারে পৃথিবীর অন্তস্তলে গিয়ে পৌঁছেছে। আমার সাইকলের ল্যাম্পটা হাতে নিয়ে এসব গহ্বরের আনাচে-কানাচে ঘোরাফেরা করে আমি গভীর আনন্দ পাই। গহ্বরের ছাতে আলো ফেললে দেখা যায় স্ট্যাল্যাক্টাইটের কালোর ফাঁকে ফাঁকে রুপালির ঝলমলানি। আলো নেভালে দুর্ভেদ্য অন্ধকার, জ্বালালে আরব্যোপন্যাসের মায়াপুরীর বর্ণচ্ছটা।
এইসব ফাটলের মধ্যে একটির বিশেষত্ব হল এই যে, সেটা মানুষের কীর্তি, প্রকৃতির নয়। বু-জনের কথা আমি এখানে আসার আগে শুনিনি। এক জাতীয় নীল রঙের খনিজ পদার্থের নাম। হল ব্লু-জন। এই ধাতু এতই দুষ্প্রাপ্য যে, এর তৈরি একটা ফুলদানিই বিক্রি হয় আগুনের দামে। আশ্চর্য অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন রোমানরাই প্রথম এই অঞ্চলে ব্লু-জনের অস্তিত্ব অনুমান করে পাহাড়ের গায়ে একটা গভীর সুড়ঙ্গ খনন করে। আগাছার জঙ্গলে আবৃত এই সুড়ঙ্গের মুখটাকেই বলা হয় রু-জন গ্যাপ। রোমানদের এই কীর্তির তারিফ না করে উপায় নেই। নোনা-ধরা অনেক গহ্বর ভেদ করে চলে গেছে এই সুড়ঙ্গ। অতি সন্তর্পণে, অনেক মোমবাতি হাতে মজুত রেখে এই সুড়ঙ্গে প্রবেশ না করলে, এর অন্ধকার জগৎ থেকে আবার বাইরের আলোয় বেরিয়ে আসা একেবারে অসম্ভব। আমি এখন পর্যন্ত বেশিদূর এগোইনি, তবে আজই সকালে এর মুখটায় দাঁড়িয়ে গহ্বরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আমার স্বাস্থ্য ফিরে পেলে কোনও এক ছুটির দিনে এসে, রোম্যানরা ডার্বিশায়ারের পাহাড় ভেদ করে কতদূর ঢুকতে পেরেছিল, সেটা যাচাই করে দেখব।
এখানকার লোকেরা যে কী পরিমাণ কুসংস্কারে বিশ্বাসী তা ভাবলে অবাক লাগে। এমনকী আর্মিটেজ ছোক্রাটিও দেখলাম বাদ যায় না। অথচ সে তো বেশ সুস্থ সবল শিক্ষিত লোক, আর মানুষ হিসেবেও চমৎকার। আমি গহুরটার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় দেখি সে সামনের মাঠ পেরিয়ে আমারই দিকে আসছে। এসে বলল, ডাক্তারবাবুর দেখছি এ ব্যাপারে তেমন ভয়ডর নেই।
আমি একটু অবাক হয়েই বললাম, ভয়? কীসের ভয়?
আর্মিটেজ গহ্বরের অন্ধকারের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, ওই যিনি থাকেন ওর ভিতরে–তাঁর!
এইসব পাণ্ডববর্জিত গ্রামদেশে উদ্ভট সব কিংবদন্তি গড়ে ওঠা বোধহয় খুব সহজ, আমি আর্মিটেজকে জেরা করে তার এই অদ্ভুত ধারণার কারণ জানলাম। সে বলল প্রায়ই নাকি গ্রামের এখান-সেখান থেকে একটি-আধটি করে ভেড়া উধাও হয়ে যায়। আর্মিটেজের মতে নাকি সেগুলোকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তারা যে আপনা থেকেই ভুল পথে চলে গিয়ে পাহাড়ের খাদে-খন্দে হারিয়ে যেতে পারে, সে কথা বলতে আর্মিটেজ বলল, একবার নাকি এক চাপ রক্ত ও একগোছা ভেড়ার নোম পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছিল। এই ঘটনারও যে একটা অত্যন্ত সাধারণ কারণ থাকতে পারে, সেটা বলতে আর্মিটেজ পালটা জবাব দিল যে, ভেড়াগুলো উধাও হয় নাকি কেবলমাত্র অমাবস্যার রাত্রে। তাতে আমি বললাম যে, এসব অঞ্চলে যদি ভেড়া-চোর থেকে থাকে, তা হলে তারা তাদের কাজের জন্য যে অমাবস্যার রাতটাই বেছে নেবে, তাতে আর আশ্চর্য কী? জবাবে আর্মিটেজ বলল, একবার নাকি দেখা গিয়েছিল গ্রামের একটা পাঁচিলের গা থেকে কে যেন বড় বড় পাথরের ইট সরিয়ে সেগুলোকে বহুদূরে ছড়িয়ে ফেলে রেখে এসেছে। আমার মতে এ কাজও অবিশ্যি মানুষের অসাধ্য নয়। কিন্তু সবশেষে আর্মিটেজ এক তুরুপ মেরে বসল। সে বলল সে নাকি এই অদৃশ্য প্রাণীটির গর্জন শুনতে পেয়েছে। গহ্বরের মুখে একটানা বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেই নাকি সে-শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। আর বহুদুর থেকে এলেও সে-শব্দের জোর নাকি সহজেই অনুমান করা যায়। কথাটা শুনে আমি না হেসে পারলাম না। আমি জানতাম যে পাহাড়ের ভিতর যদি জল চলাচল করে, তা হলে লাইমস্টোনের ফাঁকে ফাঁকে সেই জলপ্রবাহের শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে বাইরে থেকে গর্জনের মতো শোনানো কিছুই আশ্চর্য নয়। এভাবে বারবার তার কথার প্রতিবাদ করায় আর্মিটেজ শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে আমায় ছেড়ে চলে গেল।
আর তার পরমুহূর্তে ঘটল এক আশ্চর্য ঘটনা। আমি গহ্বরের মুখটায় দাঁড়িয়ে, আর্মিটেজের কথাগুলো কত সহজে হেসে উড়িয়ে দেওয়া গেল তাই ভাবছি, এমন সময় সত্যিই গহ্বরের ভিতর থেকে এল এক অদ্ভুত শব্দ। সেশব্দের সঠিক বর্ণনা দেব কী করে? প্রথমত, শুনে মনে হল সেটা আসছে বহুদূর থেকে–যেন পৃথিবীর একেবারে গভীরে অবস্থিত কোনও জায়গা থেকে। কিন্তু দূর থেকে এলেও শব্দটা রীতিমতো জোরে। জলধারা বা পাথর গড়িয়ে পড়া থেকে যে শব্দ হয়, এটা সে জাতের নয়। এ-যেন এক তীব্র, তীক্ষ্ণ হ্রেষাধ্বনির মতো। এই আশ্চর্য অভিজ্ঞতার ফলে কিছুক্ষণের জন্য আর্মিটেজের কথাগুলো আমাকে নতুন করে ভাবিয়ে তুলল। আমি আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক গহ্বরের মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম, কিন্তু দ্বিতীয়বার আর সে-শব্দ শোনা গেল না। বাড়ি ফিরলাম মনে গভীর বিস্ময়ের ভাব নিয়ে। আর্মিটেজের কথায় আমল দেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু এটা অস্বীকার করা চলে না যে, যে-শব্দটা আমি নিজের কানে শুনেছি, সেটা ভারী অদ্ভুত। এখনও লিখতে লিখতে যেন কানে সেশব্দটা শুনতে পাচ্ছি।
এপ্রিল ২০
গত তিন দিনে আমি বার কয়েক ব্লু-জন গ্যাপের দিকে গিয়েছি। এমনকী, সুড়ঙ্গের ভিতরেও কিছুদূর অগ্রসর হয়েছি। কিন্তু আমার ল্যাম্পের আলো যথেষ্ট জোরালো না হওয়ায় বেশিদূর যেতে সাহস পাইনি। এবারে আরও আঁটঘাট বেঁধে যেতে হবে। শব্দটা আর দ্বিতীয়বার শোনার সৌভাগ্য হয়নি। এক-একবার মনে হয়েছে যে, প্রথমবারে শোনাটা হয়তো আমার আর্মিটেজের সঙ্গে কথাবার্তার ফলে আমার কল্পনাপ্রসূত। সমস্ত ব্যাপারটাই যে আজগুবি সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। যদিও এটা না বলে পারছি না যে, গ্যাপের মুখে ঝোঁপঝাড়ের অবস্থা দেখে এক-এক সময় মনে হয়েছে যে, কোনও অতিকায় জীব হয়তো তার মধ্য দিয়ে পথ করে নিয়ে যাতায়াত করছে। মোট কথা, আমার মনে একটা তীব্র কৌতূহল জেগে উঠেছে। অ্যালারটনদের আমি এখনও কিছু বলিনি, কারণ এঁরাও কুসংস্কার থেকে মুক্ত নন। কিন্তু আমি নিজে আরও অনুসন্ধান করব, আর তার। জন্য কিছু মোমবাতিও কিনে রেখেছি।
আজ সকালে গ্যাপের কাছাকাছি ঝোঁপের আশেপাশে কিছু ভেড়ার লোম পড়ে থাকতে দেখলাম। একটা লোমের গোছায় দেখি রক্ত লেগে রয়েছে। বেশ বুঝতে পারি যে, পাথুরে জায়গায় চরে বেড়ালে ভেড়াগুলো আপনা থেকেই জখম হতে পারে, কিন্তু তাও হঠাৎ ওই লালের ছোপ চোখে পড়াতে কেমন যেন চমকে উঠলাম। রোমানদের কারুকার্যে শোভিত গহ্বরের ওই প্রবেশদ্বার মনের মধ্যে একটা অজানা আতঙ্কের সঞ্চার করল। গহ্বরের অন্ধকারের ভিতর থেকে যেন আদ্যিকালের একটা ভ্যাপসা গন্ধ আসছে। সত্যিই কি কোনও নাম-না-জানা প্রাণী ওই অন্ধকারের মধ্যে বাস করে? সুস্থ অবস্থায় হয়তো এসব চিন্তা মাথায় আসত না। অসুখে মানুষের স্নায়ু দুর্বল হয়ে পড়ে, আর তাই তার মনে নানান অসম্ভব কল্পনা দানা বাঁধতে পারে।
এইসব ভীতিজনক চিন্তা আমার সঙ্কল্পকে শিথিল করে দিয়েছিল। ভেবেছিলাম, গহ্বরের রহস্য রহস্যই থাক, এ নিয়ে আর মাথা ঘামাব না। কিন্তু আজ রাত্রে আবার নতুন করে উৎসাহ জেগে উঠেছে, আর মনেও অনেকটা জোর পাচ্ছি। আশা করি, কাল এব্যাপারে আরও কিছুদুর অগ্রসর হতে পারব।
এপ্রিল ২২
আমি যথাসাধ্য পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে কালকের অদ্ভুত অভিজ্ঞতাটা বর্ণনা করার চেষ্টা করছি। কাল যখন আমি ব্লু-জন গ্যাপের উদ্দেশে রওনা দিই, তখন বিকেল। বলতে দ্বিধা নেই, সেখানে পৌঁছে। গহ্বরের দুর্ভেদ্য অন্ধকারের দিকে চাইতেই আবার যেন সেই আশঙ্কার ভাবটা আমার মনে জেগে উঠল। মনে হল, একা না এসে একজন সঙ্গী আনা বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হত। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত মনে সাহস ফিরিয়ে এনে মোমবাতি জ্বেলে কাঁটা-ঝোঁপের জঙ্গল ভেদ করে গহ্বরের ভিতর ঢুকলাম।
আলগা পাথরের ঢাকা জমির উপর দিয়ে প্রায় পঞ্চাশ ফুট নামার পর একটা রাস্তা পেলাম, যেটা একেবারে পাহাড় ভেদ করে সোজা সামনের দিকে চলে গেছে। যদিও আমি জিওলজিস্ট নই, তবু এটুকু বুঝতে পারলাম যে, এ পাথর লাইমস্টোনের চেয়ে অনেক বেশি শক্ত জাতের কোনও পাথর, কারণ এর গায়ে প্রাচীন শাবলের দাগ রয়েছে। দেখলে মনে হয় যেন এই সবেমাত্র খোঁড়া হয়েছে। আমি কোনওমতে হোঁচট খেতে খেতে এই প্রাচীন পাথরের সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললাম। আমার হাতের মোমবাতি আমাকে ঘিরে একটা ক্ষুদ্র আলোর গণ্ডি রচনা করেছে। তার ফলে সামনের সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় পৌঁছে দেখি সেটা গিয়ে পড়েছে একটা বিশাল নোনা-ধরা পাথরের গহ্বরে, যার ছাত থেকে ঝুলে আছে চুনে-ঢাকা অসংখ্য লম্বা-লম্বা আইসি। আবছা আলোয় আরও লক্ষ করলাম যে, গহ্বরের দেওয়াল ভেদ করে চারদিক দিয়ে আরও অনেকগুলো জলে-ক্ষয়ে-যাওয়া রাস্তা এঁকেবেঁকে কোথায় যেন গিয়েছে। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরও এগোব না ফিরে যাব তাই ভাবছি, এমন সময় আমার পায়ের কাছে একটা জিনিস প্রবলভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।
গহ্বরের মেঝেয় অধিকাংশটাই হয় পাথর না হয় চুনের আবরণে ঢাকা; কিন্তু একটা জায়গায় বেশ খানিকটা অংশ জুড়ে ছাত থেকে জল ছুঁইয়ে পড়ে কাদা হয়ে আছে। সেই কাদার ঠিক মাঝখানে দেখলাম একটা প্রকাণ্ড ছাপ, অস্পষ্ট অথচ গভীর। উপর থেকে পাথরের চাঁই পড়লে যেরকম হয় অনেকটা সেইরকম। কিন্তু কাছাকাছির মধ্যে কোনও আগা পাথর বা এমন কিছু লক্ষ করলাম না, যাকে ওই ছাপের জন্য দায়ী করা চলে। অথচ কোনও পরিচিত জন্তুর এতবড় পায়ের ছাপ পড়া সম্ভব নয়। আর জন্তুই যদি হয়, তা হলে মাত্র একটা পায়ের ছাপ কেন? যতখানি জায়গা জুড়ে কাদা হয়েছে, কোনও চেনা জন্তু অন্তত আর-একটা ছাপ না ফেলে অতখানি জায়গা পেরোতে পারে না। যাই হোক, আমি ওই আশ্চর্য ছাপটা পরীক্ষা করে উঠে দাঁড়িয়ে, চারদিকে অন্ধকারের দিকে চেয়ে বুঝতে পারলাম আমার বুকের ভিতরে একটা দুরু দুরু কাঁপুনি শুরু হয়েছে, আর তার সঙ্গে আমার হাতের মোমবাতিটাও কিছুতে স্থির রাখতে পারছি না।
অবশেষে নিজের মনকে বোঝালাম যে, অতবড় ছাপ যখন কোনও পরিচিত জানোয়ারের হতে পারে না–এমনকী হাতিরও নয়, তখন এ ধরনের অমূলক কল্পনাকে প্রশ্রয় দেওয়া মানে আমার কাজের ব্যাঘাত ঘটানো ছাড়া আর কিছুই নয়। আরও এগোনোর আগে আমি একবার যে সুড়ঙ্গটা দিয়ে গহ্বরে এসে পৌঁছেছি, তার মুখের চেহারাটা ভাল করে দেখে চিনে রাখলাম। এ কাজটা খুবই দরকারি, কারণ এটা ছাড়া আরও অনেকগুলো রাস্তা গহ্বর থেকে বেরিয়েছে। কোথায় ফিরতে হবে সেটা জেনে নিয়ে, অবশিষ্ট মোমবাতি ও দেশলাই-এর কাঠিগুলো একবার পরীক্ষা করে, আমি অসমতল পাথরের উপর দিয়ে গহ্বরের ভিতর এগিয়ে চললাম।
রওনা হওয়ার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আচমকা এক চরম বিপদের সামনে পড়তে হল। আমার সামনে দিয়েই বয়ে চলেছিল প্রায় বিশ ফুট চওড়া একটা নালা। সেটাতে পা না ভিজিয়ে টপকে পার হওয়া যায় কোনখান দিয়ে, সেটা দেখবার জন্য আমি জলের ধার দিয়ে হেঁটে চলেছি, এমন সময় নালার উপর একটা পাথরের ঢিপি চোখে পড়ল। আন্দাজে মনে হল এক লাফে সেই টিপিটার উপর পৌঁছনো যায়। কিন্তু পাথরের তলার দিকটা জলে ক্ষয়ে যাওয়ার ফলে সেটার উপর লাফ দিয়ে। পড়তেই পাথরটা কাত হয়ে আমায় ফেলে দিল একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা নালার জলে। মোমবাতিটা নিভে গেল সঙ্গে সঙ্গেই, আর আমি ঘুটঘুঁটে অন্ধকারে জলের মধ্যে পড়ে অসহায়ভাবে এদিক ওদিক হাতড়াতে লাগলাম।
শেষটায় কোনওরকমে দাঁড়িয়ে উঠে নিজের গোঁয়ার্তুমির কথা ভেবে ভয়ের চেয়ে হাসিই পেল বেশি। জ্বলন্ত মোমবাতিটা অবশ্যই জলে পড়ে খোয়া গেছে, কিন্তু আমার পকেটে রয়েছে আরও। দুটো, কাজেই চিন্তা নেই। একটা মোমবাতি বার করে সেটা জ্বালাতে গিয়ে বুঝতে পারলাম বিপদটা কোথায়; জলে পড়ার ফলে আমার দেশলাইয়ের বাক্সটা ভিজে একেবারে সপে হয়ে গিয়েছে, ফলে সেটাতে আর কোনও কাজই হবে না।
এবার সত্যি করেই আমার রক্ত হিম হয়ে এল। অন্ধকারের নমুনাটাও এবার বেশ বুঝতে পারলাম। চারদিক থেকে সে অন্ধকার যেন আমায় ঘিরে চেপে ধরেছে; হাত দিয়ে যেন সে অন্ধকারের ঘনত্ব অনুভব করা যায়। আমি কোনওরকমে নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করলাম। গহ্বরের কোনদিকে কী আছে সেটা প্রাণপণে মনে করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু সে চেষ্টাও বৃথা কারণ চিনে রাখার মতো যা কিছু দেখে রেখেছিলাম, তা সবই দেওয়ালের উপর দিকে–সুতরাং মেঝে হাতড়ে কোনও ফলই হবে না। তাও, হয়তো দেওয়ালের গায়ে হাত বুলিয়ে সাবধানে এগোলে আবার রোমান সুড়ঙ্গর মুখটায় পৌঁছনো যেতে পারে, এই মনে করে আমি এক পা দু পা করে দেওয়ালের দিক আন্দাজ করে এগোতে লাগলাম। অচিরেই বুঝতে পারলাম, এ চেষ্টায় কোনও ফল হবে না। ওই বেয়াড়া অন্ধকারে দশ বারো পা হাঁটার পরেই বুঝলাম যে, এ অবস্থায় দিক্বিদিজ্ঞান বজায় রাখা অসম্ভব। নালার কুলকুল শব্দ থেকে অবশ্য বুঝতে পারছিলাম সেটা কোনখান দিয়ে বইছে–কিন্তু সেটা থেকে সামান্য দূরে গেলেই নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় মনে হচ্ছিল। বুঝলাম এ অবস্থায় গহ্বর থেকে বেরোনোর কোনও উপায় নেই।
আমি আবার সেই পাথরটার উপর বসে আমার শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে ভাবতে আরম্ভ করলাম। আমি যে ব্লু-জন গহুরে অভিযানের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিলাম, সে কথা আমি কাউকে বলিনি। সুতরাং আমি হারিয়ে গেলেও আমাকে খুঁজতে কোনও সার্চ-পার্টি যে এদিকে আসবে এমন কোনও আশা নেই। একমাত্র নিজের উপস্থিত বুদ্ধি ছাড়া আমার আর কোনও অবলম্বন নেই। মুক্তির উপায় যেটা রয়েছে, সেটা হল কোনও একটা পন্থা বার করে দেশলাইগুলোকে শুকিয়ে নেওয়া। আমি যখন জলে পড়েছিলাম, তখন আমার শরীরের একটা দিকই ভিজেছিল। বাঁ দিকের কাঁধটা জলের উপরে ছিল। আমি দেশলাইয়ের বাক্সটা বার করে সেটাকে আমার বাঁ বগলের তলায় চেপে বসে রইলাম। শরীরের উত্তাপ সেটাকে শুকোনোর কাজে নিশ্চয়ই কিছুটা সাহায্য করবে। তবে কমপক্ষে ঘণ্টাখানেকের আগে মোমবাতি জ্বালানোর কোনও সম্ভাবনা নেই এবং এই ঘন্টাখানেক চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া আর কোনও গতি নেই।
আসবার সময় কিছু বিস্কুট পকেটে পুরে এনেছিলাম, তারই একটা মুখে পুরে চিবোতে লাগলাম। বিস্কুটের শুকনো ভাবটা কাটানোর জন্য যে নালায় আমার পতন হয়েছিল, তারই খানিকটা জল আঁজলা করে তুলে মুখে ঢেলে দিলাম।
খাওয়া শেষ হলে পর নিজের শরীরটাকে ঢিপির উপর একটু এদিক-ওদিক নেড়ে ঠেস দেওয়ার একটা জায়গা বার করে, পা ছড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়লাম। গহ্বরের স্যাঁতস্যাঁতে ঠাণ্ডাটা বেশ তীব্রভাবেই অনুভব করছিলাম, কিন্তু মনকে বোঝালাম যে, আধুনিক চিকিৎসকদের মতে আমার যে রোগ, তাতে জানলা খুলে শোয়া, এবং শীত-গ্রীষ্ম নির্বিশেষে প্রাকৃতিক পরিবেশে বিচরণ–এ দুটোর কোনওটাই নিষিদ্ধ নয়। ক্রমে গহ্বরের দুর্ভেদ্য অন্ধকার ও নালার একঘেঁয়ে কুলকুলুনি আমায় তন্দ্রাচ্ছন্ন করে ফেলল।
কতক্ষণ এইভাবে ছিলাম জানি না। ঘণ্টাখানেক কিংবা তারও হয়তো কিছু বেশি হবে। এমন সময় হঠাৎ আমাকে সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে ঢিপির উপর সোজা হয়ে উঠে বসতে হল। আমার কানে একটা শব্দ এসেছে, যেটা নালার শব্দের চেয়ে একেবারে আলাদা। শব্দটা এখন আর নেই, কিন্তু তার প্রতিধ্বনি এখনও আমার কানে বাজছে। এটা কি মানুষের পায়ের শব্দ? আমাকে খুঁজতে এসেছে। কি কোনও দল? কিন্তু তাই যদি হয় তা হলে তো তারা আমার নাম ধরে ডাকবে। যা শুনেছি তা তো মানুষের গলার শব্দ নয়! আমি দুরু দুরু বক্ষে দম প্রায় বন্ধ করে বসে রইলাম। ওই যে–আবার সেই শব্দ! ওই–আবার! এবার আর থামা নেই। একটানা শব্দ আসছে–কোনও জানোয়ারের পদক্ষেপের শব্দ–দুম দুম দুম দুম্! কী বিশাল এই পদধ্বনি! জানোয়ারটি যে আয়তনে বিরাট, তাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু মনে হয় পায়ের তেলোগুলো নরম হওয়ার ফলে শব্দটা খানিকটা চাপা। এই অন্ধকারেও সেই পদক্ষেপে বিন্দুমাত্র ইতস্তত ভাব নেই। আর এতেও কোনও সন্দেহ নেই যে, সেটা আমার দিকেই আসছে।
পায়ের আওয়াজ শুনতে শুনতে আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে এল। কোনও অজ্ঞাত প্রাণী অন্ধকারের বাধা অগ্রাহ্য করে এগিয়ে আসছে। আমি পাথরের উপর সটান শুয়ে পড়ে নিজেকে যথাসম্ভব অদৃশ্য করে ফেলার চেষ্টা করলাম। শব্দটা এগিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ থেমে গেল। তারপর শুরু হল একটা সপাৎ সপাৎ আওয়াজ। জন্তুটা নালার জল খাচ্ছে। তারপর একটুক্ষণ চুপচাপ, কেবল মধ্যে মধ্যে প্রচণ্ড নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ, আর নাক টেনে গন্ধ শোঁকার শব্দ। জন্তুটা কি আমার অস্তিত্ব টের পেয়ে গেল নাকি? আমার নিজের নাক তখন একটা বিশ্রী বুনো গন্ধে ভরে আছে। তারপর আবার শুরু হল পায়ের শব্দ, আর সেটা যেন নালার এদিকে আমার কাছেই। আমার হাতকয়েকের মধ্যে কিছু আলগা পাথর খড়বড় করে উঠল। আমি নিশ্বাস বন্ধ করে পাথরের উপর ঘাপটি মেরে বসে রইলাম। তারপর শুনলাম পায়ের শব্দ পিছিয়ে যাচ্ছে। জলের ছপছপানি শুনে বুঝলাম, জন্তুটা নালা পেরিয়ে উলটো দিকে চলে যাচ্ছে। ক্রমে যেদিক দিয়ে শব্দটা এসেছিল সেইদিকেই আবার সেটা মিলিয়ে গেল।
আমি বেশ কিছুক্ষণ পাথরের উপর পড়ে রইলাম। ভয়ে নড়বার শক্তি ছিল না। শব্দটার কথা বারবার মনে পড়তে লাগল, আর আর্মিটেজের আতঙ্কের কথা, আর নরম কাদার উপর সেই বিরাট পায়ের ছাপের কথা।
এখন আর কোনও সন্দেহ নেই যে, পাহাড়ের এই গহ্বরে কোনও এক নাম-না-জানা, ভয়াবহ, অতিকায় প্রাণী বাস করছে। সেটা যে কেমন দেখতে, তা এখনও অনুমান করতে পারিনি, তবে এটুকু জানি যে, সেটা আয়তনে বিরাট এবং আশ্চর্য দ্রুতগতি। সাধারণ বুদ্ধিতে বলে, এমন জানোয়ার অসম্ভব, কিন্তু আমার আজকের অভিজ্ঞতা এর বিপরীত সাক্ষ্য দিচ্ছে। এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব আমার মনকে অস্থির করে তুলল। অবশেষে মনকে বোঝালাম যে, আমি নিশ্চয়ই স্বপ্ন দেখেছি। আমার রুগণ অবস্থাই আমার মনে এক কাল্পনিক বিভীষিকার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু, এবার যে ঘটনাটা ঘটল, তাতে আমার মনে আর সন্দেহের কোনও কারণই রইল না।
আমার দেশলাই এতক্ষণে শুকিয়েছে মনে করে আমি বগল থেকে সেটা বার করে একটা কাঠি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম। গহ্বরের ফাটলে হাত ঢুকিয়ে বাক্সের গায়ে কাঠি ঘষতেই সেটা ফস্ করে জ্বলে ইঠল। মোমবাতি জ্বালিয়ে, যেদিকে জানোয়ার গেছে সেদিকে একবার ভয়ে ভয়ে দেখে নিয়ে রোমান সুড়ঙ্গের দিকে রওনা দিলাম। যাওয়ার পথে জমির নরম অংশটাতে চোখ পড়তেই দেখলাম, আগের ছাপের মতো আরও তিনটে টাটকা ছাপ সেখানে পড়েছে, সেইরকমই গভীর আর সেইরকমই বিরাট। এ-দৃশ্যে আবার নতুন করে যেন ভয়ে আমার হৃৎকম্প শুরু হল। আমি মোমবাতির শিখাটাকে হাত দিয়ে আড়াল করে প্রাণপণে সুড়ঙ্গপথ দিয়ে দৌড়ে গিয়ে, এক নিশ্বাসে দরজার মুখ দিয়ে বেরিয়ে কাঁটাঝোঁপ ভেদ করে হাঁপাতে হাঁপাতে বাইরের ঘাসের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লাম। মাথার উপর আকাশে তখন অজস্র তারা ঝলমল করছে।
বাড়ি পৌঁছলাম রাত তিনটায়। আজ এখন পর্যন্ত আমার স্নায়ুর রন্ধ্রে রন্ধ্রে আতঙ্ক ও উত্তেজনার শিহরন রয়েছে। কিন্তু এখনও আমি কাউকে কিছু বলিনি। এব্যাপারে খুব সাবধানে এগোতে হবে। এখানকার সরল গ্রাম্য অধিবাসীরা, বা নিরীহ অ্যালারটন ভগিনীদ্বয়, আমার এ ঘটনা শুনলে কী মনে করবে জানি না। আমার এখন এমন কারুর কাছে যাওয়া উচিত, যাকে ঘটনাটা বললে সে একটা উপায় বাতলাতে পারবে।
এপ্রিল ২৫
গহ্বরের অভিজ্ঞতার পর দুদিন আমি শয্যাশায়ী ছিলাম। গত ক দিনের মধ্যে আমার এমন আর একটা অভিজ্ঞতা হয়েছে, যাতে অন্যটার চেয়ে কিছু কম ধাক্কা খাইনি। আগেই বলেছি, আমি এমন। একজনের অনুসন্ধান করছিলাম, যে আমাকে কিছুটা পরামর্শ দিতে পারবে। এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে মার্ক জনসন বলে এক ডাক্তার থাকেন। প্রফেসর স্যান্ডারসন এই ডাক্তারটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে একটা চিঠি আমাকে দিয়ে দিয়েছিলেন। আমি একটু সুস্থ হয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ঘটনাটা খুলে বললাম। তিনি মনোযোগ সহকারে সবকিছু শোনার পর আমার স্নায়বিক প্রতিক্রিয়া ও আমার চোখের মণি খুব ভাল করে পরীক্ষা করে দেখলেন। দেখা শেষ হলে পর তিনি কোনও আলোচনার দিকে না গিয়ে সোজাসুজি বললেন যে, আমার ব্যাপারটা সম্পূর্ণ তাঁর আওতার। বাইরে। তবে কাসলটনে মিঃ পিটন বলে এক ভদ্রলোক থাকেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করে আমার ঘটনাটা তাঁকে আদ্যোপান্ত জানানো দরকার। তিনিই নাকি একমাত্র ব্যক্তি, যিনি আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করতে পারেন।
অগত্যা, স্টেশন থেকে দশ মাইল দূরে একটা ছোট্ট শহরে গিয়ে হাজির হতে হল। শহরের এক প্রান্তে একটা সম্রান্ত অট্টালিকার সামনে গেটের গায়ে পিতলের ফলকে পিল্টনের নাম দেখে বুঝলাম তিনি এখানকার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। দরজায় বেল-টা টেপার সময় মনে কেমন যেন একটা খটকা লাগল। কাছাকাছি একটা দোকানে গিয়ে মালিককে পিটন সাহেব সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায়। তিনি একগাল হেসে বললেন, সে কী, জানেন না? উনি যে এ-তল্লাটে সবচেয়ে নামকরা মাথার ব্যানোর ডাক্তার! ওই তো ওর পাগলা গারদ। বলা বাহুল্য, আমি আর এক মুহূর্তও সেখানে
থেকে সোজা আমার গ্রামে ফিরে এলাম। চুলোয় যাক এইসব পণ্ডিত লোক। এঁরা যেন এঁদের জ্ঞানের সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে কোনও কিছুই স্বীকার করতে চান না। অবশ্য, এখন ঠাণ্ডা মাথায় বুঝতে পারছি যে, আমি আর্মিটেজের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছি, জনসনও আমার সঙ্গে ঠিক সেই একই ব্যবহার করেছেন।
এপ্রিল ২৭
ছাত্রাবস্থায় সাহস ও উদ্যমের জন্য আমার বেশ খ্যাতি ছিল। একবার কোল্টব্রিজের এক হানাবাড়িতে রাত কাটাবার কথা উঠলে আমিই প্রথম এগিয়ে গিয়েছিলাম। এখন আমার বয়স পঁয়ত্রিশ। তা হলে কি বয়স বাড়ার ফলেই আমার সাহস কমেছে, না কি আমার রোগই এর কারণ? গহুর আর তার অধিবাসীর কথা ভাবলে এখনও আমার মনে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। এ অবস্থায় কী করা যায়, এ প্রশ্ন প্রতি মুহূর্তেই আমাকে ভাবিয়ে তুলছে। কাউকে কিছু না বলে যদি চুপচাপ বসে থাকি, তা হলে হয়তো গহ্বরের রহস্য চিরকাল রহস্যই থেকে যাবে। আবার যদি সকলের কাছে সব কিছু প্রকাশ করে ফেলি, তা হলে হয়তো সারা গ্রাম জুড়ে একেবারে আতঙ্কের বন্যা বয়ে যাবে। আর না হয় তো এরা আমাকে পাগল ভেবে সেই গারদেই চালান দেবে। সবচেয়ে ভাল পন্থা বোধহয়। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করে আরও ভালভাবে আঁটঘাট বেঁধে আর একবার গহ্বরে অভিযান। আমি এর মধ্যেই কালটনে গিয়ে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করে এনেছি। তার মধ্যে প্রধান হল একটা অ্যাসিটিলিন ল্যাম্প ও একটা দোনলা বন্দুক। দ্বিতীয়টা অবশ্য ধার করতে হয়েছে, কিন্তু এক ডজন ভাল কার্তুজ আমি নিজে পয়সা খরচ করে কিনেছি। যা আছে, তাতে একটা আস্ত গণ্ডার অনায়াসে ধরাশায়ী করা চলে। মোট কথা, আমার গুহাবাসী বন্ধুটির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমি। প্রস্তুত। কিছুটা স্বাস্থ্যোন্নতি ও আরও খানিকটা মনের জোর পেলেই আমি যুদ্ধং দেহি বলে বেরিয়ে পড়ব। কিন্তু আপাতত, এই জানোয়ারটি ঠিক কোন জাতের সে প্রশ্নে আমার ঘুম নষ্ট হতে চলেছে। একের পর এক নানান জবাব আমি নিজেই বাতিল করে দিয়েছি। ভেবে ভেবে কোনও কূল-কিনারা পাচ্ছি না। এটা যে একটা রক্তমাংসের জ্যান্ত জানোয়ার, সেটা তো তার চিৎকার আর তার পায়ের ছাপ থেকেই প্রমাণ হয়। তা হলে কি হিংস্র ড্রাগন জাতীয় যেসব প্রাণীর কথা আমরা রূপকথায় পড়েছি, সেগুলো আসলে কাল্পনিক নয়? তাদের খানিকটা অংশ কি আসলে সত্যি, এবং সেই সত্যটুকু প্রমাণ করার ভার কি শেষটায় আমার উপর পড়ল?
৩ মে
কদিন যাবৎ এখানকার বসন্তকালের খামখেয়ালি আবহাওয়াটা আমাকে বেশ কাবু করেছে। আর এই কদিনের ভিতরই এমন কিছু উদ্ভট ঘটনা ঘটেছে, যার তাৎপর্য কেবল আমিই বুঝি। রাতগুলো মেঘলা হওয়ায় তিনদিন চাঁদের আলো ছিল না। এর আগে ঠিক এমন রাত্রেই একটি ভেড়া উধাও হয়েছে। গত কয়েক রাত্রেও ভেড়া লোপ পেয়েছে–অ্যালারটনদের দুটি, ক্যাটওয়াকের বুড়ো পিয়ার্সনের একটি ও মিসেস মুলটনের একটি। তিন রাত্রে চারটি ভেড়া উধাও। কোনও চিহ্নই পাওয়া যায়নি সেগুলোর, ফলে চতুর্দিকে নানারকম গুজব রটছে। কেউ বলে এটা ভেড়া-চোরের কাজ, কেউ বলে আশেপাশে নাকি বেদেরা আস্তানা গেড়েছে–এ হল তাদেরই কীর্তি।
কিন্তু এর চেয়েও গুরুতর একটা ঘটনা ঘটেছে গত কদিনের মধ্যে; আর্মিটেজ নিখোঁজ। গত বুধবার রাত্রে সে নাকি তার বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল; তারপর থেকে তার আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। আর্মিটেজের আত্মীয়স্বজন নেই, তাই তার অন্তর্ধান তেমন একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেনি। লোকে বলছে সে নাকি অনেক টাকা ধারত, তাই অন্য কোনও জায়গায় চাকরি নিয়ে চলে গেছে–সেখান থেকে কদিনের মধ্যেই হয়তো তার জিনিসপত্র চেয়ে পাঠাবে। আমার নিজের কিন্তু অন্যরকম আশঙ্কা হচ্ছে। আমার বিশ্বাস ভেড়া-চুরির ব্যাপারটার কোনও একটা বিহিত করতে গিয়েই সে প্রাণ হারিয়েছে। হয়তো সে ওই অজ্ঞাত জীবটির অপেক্ষায় ওত পেতে বসে ছিল, আর সেটা উলটে তাকেই আক্রমণ করে তার গহ্বরের ডেরায় নিয়ে গিয়ে ফেলেছে। বিংশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের মতো সভ্য দেশে এ ধরনের ঘটনা ভাবতেও অবাক লাগে, যদিও আমার মতে এটা মোটেই অসম্ভব নয়। আর সত্যিই যদি তাই হয়, তা হলে কি আমার এ ব্যাপারে একটা দায়িত্ব নেই? আমি যখন এতদূরই জেনেছি, তখন আমার কর্তব্য এটার একটা প্রতিকারের চেষ্টা করা–সম্ভব হলে নিজেই। আজকের একটা ঘটনার পর আমি স্থির করেছি, নিজেই এব্যাপারে একটা কিছু করব। সকালে স্থানীয় পুলিশ-স্টেশনে গিয়েছিলাম। ইনস্পেক্টর সাহেব গম্ভীর ভাবে আমার বক্তব্য একটা মোটা খাতায় তুলে নিয়ে আমাকে নমস্কার করে বিদায় দিলেন। বাইরে বেরোতে না বেরোতে শুনতে পেলাম তাঁর অট্টহাসি। বুঝতে পারলাম, তিনি তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের কাছে আমার কাহিনীটা বেশ রসিয়ে পুনরাবৃত্তি করছেন।
ঠিক দেড় মাস পর আমার খাটে বালিশের ওপর পিঠ দিয়ে বসে আমি আবার ডায়রি লিখছি। শরীর ও মন বিপর্যস্ত বিহুল হয়ে আছে। যে সংকটের সামনে পড়তে হয়েছিল, আর কোনও মানুষের ভাগ্যে তেমন হয়েছে কিনা জানি না। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। ব্লু-জন গ্যাপের বিভীষিকা চিরকালের মতো বিদায় হয়েছে, জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য আমার মতো রুগণ ব্যক্তির পক্ষেও কিছু করা সম্ভব হয়েছে। এইবারে যথাসম্ভব পরিষ্কার ভাবে যা ঘটেছিল, তার বিবরণ দিই।
.
৩ মের রাতটা ছিল অন্ধকার ও মেঘাচ্ছন্ন–ঠিক যেমন রাত্রে নাম-না-জানা জানোয়ারটা হানা দিতে বেরোয়। রাত এগারোটায় হাতে লণ্ঠন ও বন্দুক নিয়ে আমি বাড়ি থেকে রওয়ানা দিলাম। যাওয়ার আগে টেবিলের উপর একটা কাগজে লিখে গেলাম যে, আমি যদি না ফিরি, তা হলে যেন ব্লু-জন গ্যাপের আশেপাশে আমার অনুসন্ধান করা হয়। রোমান সুড়ঙ্গের মুখটাতে পোঁছে, কাছাকাছি একটা পাথরের ঢিপি বেছে নিয়ে লণ্ঠনের ঢাকনাটা বন্ধ করে হাতে বন্দুক নিয়ে ঢিপিটার উপর ঘাপটি মেরে বসে রইলাম।
এই বসে থাকার যেন আর শেষ নেই। উপত্যকাটার চারদিকে টিপটিপ করছে কৃষকদের বাড়ির বাতিগুলো। দূর থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ভেসে আসছে চ্যাপল-লি-ডেল গিজার ঘড়ির ঢং ঢং শব্দ। আশেপাশে অন্য লোকজন যে রয়েছে, তার চিহ্নগুলো যেন আমার একাকিত্বকে আরও করুণ ও দুর্বিষহ করে তুলছিল। এক-এক সময় মনে হচ্ছিল, আমার অভিযানে জলাঞ্জলি দিয়ে সব ছেড়ে-ছুড়ে বাড়ি ফিরে যাই। কিন্তু মানুষের মনে আত্মসম্মান বোধটা এত গভীর ও বদ্ধমূল যে, একটা কোনও সংকল্প নিয়ে একবার অগ্রসর হলে মাঝপথে ফিরে আসা ভারী মুশকিল।
সেই কারণেই সেদিন আমি গহ্বরের মুখ থেকে ফিরে আসতে পারিনি। আর যাই হোক, আমি কাপুরুষ, এ অপবাদ আমাকে কেউ দিতে পারবে না।
দূরের গিজার ঘড়িতে বারোটা বাজল। তারপর একটা, তারপর দুটো। এই সময়টা অন্ধকার সবচেয়ে গভীর। তারাহীন আকাশের নীচ দিয়ে মেঘ ভেসে চলেছে। পাহাড়ের ফাটলে কোথায়। যেন একটা প্যাঁচা ডেকে উঠল। এ ছাড়া শুধু এক ঝিরঝিরে হাওয়ার শব্দ। আর সব চুপ। এমন সময় হঠাৎ কানে এল এক পরিচিত আওয়াজ–দুম দুম দুম দুম দুম্ দুম–আর তার সঙ্গে পায়ের। ধাক্কায় পাথর গড়িয়ে যাওয়ার শব্দ। ক্রমে এদিকে আসছে শব্দটা। কাছে–আরও কাছে। এবার। সুড়ঙ্গের মুখের ঝোঁপঝাড় খচমচ করে উঠল। পরমুহূর্তেই আবছা অন্ধকারের ভিতর দিয়ে সৃষ্টিছাড়া নাম না জানা অতিকায় কী যেন একটা প্রায় নিঃশব্দ দ্রুতপদে গুহা থেকে বেরিয়ে আমার ঠিক পাশ দিয়ে গিয়ে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ভয়ে আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম। বুঝতে পারলাম, এতক্ষণ অপেক্ষা করা সত্ত্বেও, আমার মনটা এই অপ্রত্যাশিত ও ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না।
এবার আমার সমস্ত সাহস সঞ্চয় করে জানোয়ারটার ফেরার অপেক্ষায় বসে রইলাম। গহ্বরের বাইরের শান্তিময় নিরুদ্বেগ পরিবেশ থেকে বোঝবার কোনও উপায় নেই যে, এক বিপুল বিঘুঁটে প্রাণী এই সবেমাত্র সেখানে হানা দিতে বেরিয়েছে। সেটা কতদূর যাবে, কী মতলবে গেছে, কখন ফিরবে, সেসব জানার কোনও উপায় নেই। পাথরের উপর বন্দুকের নলটাকে বসিয়ে মনে মনে। প্রতিজ্ঞা করলাম যে, দ্বিতীয়বার আর সংকট-মুহূর্তে সাহস হারাব না। যত বড় দুশমনই হোক না কেন, এবার তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতেই হবে।
সজাগ থাকা সত্ত্বেও জানোয়ারটা যে কখন ফিরে এল, সেটা টেরই পাইনি। হঠাৎ সামনে চেয়ে দেখি–আবার সেই অতিকায় জানোয়ার–ঘাসের উপর দিয়ে নিঃশব্দে হেঁটে ব্লু-জন সুড়ঙ্গের দিকে আসছে। আবার অনুভব করলাম বন্দুকের ঘোড়র উপর রাখা আমার ডান হাতের তর্জনীটা অবশ হয়ে আসছে। প্রাণপণ চেষ্টা করে কোনওরকমে আমার জড় ভাবটাকে কাটিয়ে উঠলাম। ঝোঁপঝাড় ভেদ করে জানোয়ারটা গুহার ভিতর ঢুকে প্রায় অদৃশ্য হয়ে এসেছে, এমন সময় আমি বন্দুকের ঘোড়া টিপে দিলাম। বারুদের ঝলসানিতে মুহূর্তের জন্য দেখতে পেলাম এক প্রকাণ্ড, লোমশ ছাই রঙের
জানোয়ার, নীচের দিকে রঙটা ফিকে হয়ে এসেছে–বেঁটে বেঁটে বাঁকানো পায়ের উপর তার আলিসান শরীরটাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এক ঝলকের দেখা–আর তারপরেই শুনলাম খড়বড় শব্দ। আগা পাথরের উপর দিয়ে নেমে জানোয়ারটা চলেছে তার গর্তের দিকে। আমার মাথায় হঠাৎ যেন খুন চাপল। ভয়ডর সব দূর করে দিয়ে এক লাফে পাথরের উপর থেকে নেমে বন্দুক ও লণ্ঠন হাতে সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে ছুটে চললাম জানোয়ারটার উদ্দেশে।
আমার লণ্ঠনের উজ্জ্বল রশ্মি সামনের অন্ধকার ভেদ করে চলেছে। এ সেই দু সপ্তাহ আগের টিমটিমে মোমবাতির আলো নয়। কিছুটা পথ দৌড়নোর পরই জানোয়ারটাকে দেখতে পেলাম–সুড়ঙ্গের এপাশ ওপাশ জুড়ে থপথপিয়ে এগিয়ে চলেছে, তার পায়ের লম্বা ও রুক্ষ নোম চলার সঙ্গে সঙ্গে দুলছে। লোম দেখে যদিও ভেড়ার কথা মনে হয়, আয়তনে জানোয়ারটা সবচেয়ে বড় হাতির চেয়েও বেশ খানিকটা বড়–আর যত লম্বা, ততই যেন চওড়া। পাহাড়ের সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে এই বিরাট বীভৎস জানোয়ারের পিছনে ধাওয়া করার সাহস আমি কোথা থেকে পেলাম জানি না। আদিম শিকারের নেশা যখন মানুষকে পেয়ে বসে, আর সেই শিকার যদি চোখের সামনে পালায়, তা হলে মানুষ যেন দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে তার পিছনে ছোটে। দোনলা বন্দুক হাতে তাই আমি ছুটে চলেছি এই দানবের পিছনে।
জানোয়ারটা যে রীতিমতো দ্রুতগতি, সেটা আমি আগে লক্ষ করেছিলাম। এবারে বুঝলাম যে তার আর একটি মারাত্মক গুণ আছে, সেটা হল শয়তানি বুদ্ধি। হাবভাব দেখে মনে হয়েছিল, সে বুঝি প্রাণের ভয়ে পালাচ্ছে। সে যে আবার উলটোমুখে ঘুরে রুখে দাঁড়াতে পারে, সেটা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আগেই বলেছি, সুড়ঙ্গটা গিয়ে পড়েছে একটা বিরাট গহ্বরে। কিছুক্ষণ দৌড়নোর পর সেই গহুরটাতে পৌঁছতে হঠাৎ জানোয়ারটা থমকে থেমে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল।
লণ্ঠনের সাদা আলোতে তার যা চেহারা দেখলাম, তা আমি জীবনে ভুলতে পারব না। ভাল্লুকের মতো হিংস্র ভঙ্গিতে সামনের দু পা শূন্যে তুলে দাঁড়িয়ে আছে পর্বতপ্রমাণ জানোয়ারটা, আয়তনে ভাল্লুকের দশগুণ, উঁচানো দুই পায়ের থাবায় লম্বা তীক্ষ্ণ বাঁকানো নখ, বীভৎস বিকৃত হাঁ করা লাল মুখে ধারালো দাঁতের সারি। ভাল্লুকের সঙ্গে পার্থক্য কেবল একটা ব্যাপারে–যে ব্যাপারে এটার সঙ্গে পৃথিবীর আর কোনও জানোয়ারের কোনও মিল নেই–সেটা হল জানোয়ারটার ঠিকরে বেরিয়ে আসা, দৃষ্টিহীন, মণিহীন, জ্বলন্ত বলের মতো দুটো চোখ। কী দেখলাম সেটা ভাল করে বোঝার আগেই জানোয়ারটা থাবা উচিয়ে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এর পরে আমার হাত থেকে লণ্ঠনটা ছিটকে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়া ছাড়া আমার আর কিছু মনে নেই।
যখন জ্ঞান হল, তখন দেখি আমি অ্যালারটনদের বাড়িতে আমার খাটের উপর শুয়ে আছি। রু-জন গ্যাপের ঘটনাটার পর দুদিন কেটে গেছে। মাথায় চোট লেগে অজ্ঞান হয়ে, বাঁ পায়ের হাড় ও পাঁজরের দুটো হাড় ভাঙা অবস্থায় আমি সারারাত ওই গুহার মধ্যে পড়ে ছিলাম। পরদিন সকালে আমার লেখা চিঠি খুঁজে পেয়ে জনাদশেক চাষা দল বেঁধে গিয়ে আমায় খুঁজে বার করে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে। সেই থেকে সমানে নাকি আমি প্রলাপ বকেছি। জানোয়ার জাতীয় কিছুই নাকি এদের চোখে পড়েনি। আমার বন্দুকের গুলি যে কোনও প্রাণীকে জখম করেছে, তার প্রমাণ হিসাবে কোনও রক্তের চিহ্নও নাকি এরা দেখতে পায়নি। আমার নিজের অবস্থা, এবং জমিতে কিছু অস্পষ্ট দাগ ছাড়া আমার কাহিনীর সত্যতা প্রমাণ করার মতো কিছুই নাকি পাওয়া যায়নি।
এই ঘটনার পর দেড় মাস কেটে গেছে। আমি এখন বাইরের বারান্দায় বসে রোদ পোয়াচ্ছি। আমার ঠিক সামনেই খাড়া পাহাড়–তার পাংশুটে পাথরের গায়ে ওই যে দেখা যাচ্ছে র-জন সুড়ঙ্গের। মুখ। কিন্তু ওটা আর আমার মনে ভীতিসঞ্চার করে না। আর কোনওদিনও ওই সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে কোনও ভয়ঙ্কর প্রাণী মনুষ্যজগতে হানা দিতে বেরোবে না। বিজ্ঞানবি অথবা বিদ্যাদিগগজ অনেক সম্ভ্রান্ত বাবুরা হয়তো আমার কাহিনীকে হেসে উড়িয়ে দেবেন–কিন্তু এখানকার দরিদ্র সরল গ্রামবাসীরা আমার কথা এক মুহূর্তের জন্যও অবিশ্বাস করেনি। এ সম্পর্কে কালটন কুরিয়ার পত্রিকার মন্তব্য তুলে দিলাম :
আমাদের পত্রিকার, অথবা ম্যাটলক, বাক্সটন ইত্যাদি অঞ্চলের যেসব পত্রিকার সংবাদদাতা উক্ত ঘটনার তদন্ত করিতে আসিয়াছেন, তাহাদের কাহারও পক্ষে গহ্বরে প্রবেশ করিয়া ডাঃ জেস হার্ডকাসলের বিচিত্র কাহিনীর সত্যমিথ্যা বিচার করিবার কোনও উপায় ছিল না। উক্ত ঘটনা সম্পর্কে কী করণীয় তাহা স্থানীয় অধিবাসীগণ নিজেরাই স্থির করিয়া প্রত্যেকেই গুহার প্রবেশদ্বারটি প্রস্তর দ্বারা বন্ধ করিতে তৎপর হইয়াছিল। গহ্বরের সম্মুখস্থ ঢালু রাস্তা দিয়া বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড গড়াইয়া লইয়া সুড়ঙ্গ-দ্বারটি তাহারা সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে। এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটির পরিসমাপ্তি ঘটে এইভাবেই। স্থানীয় বাসিন্দাগণ ঘটনাটি সম্পর্কে বিভিন্ন মত পোষণ করেন। কেহ কেহ বলেন, রুণ অবস্থাই ডাঃ হার্ডকাসূলের মস্তিষ্কবিকৃতি ও তজ্জনিত উদ্ভট কল্পনাদির কারণ। ইহাদের মতে, কোনও ভ্রান্ত অথচ দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহাকে গহ্বরে প্রবেশ করিতে বাধ্য করিয়াছিল, এবং গহ্বরের প্রস্তর ভূমিতে পদস্খলন হেতু তিনি আহত হইয়াছিলেন। গহ্বরের ভিতর যে এক অদ্ভুত জীব বাস করে, এরূপ একটা জনপ্রবাদ বহুঁকাল হইতে এই অঞ্চলে প্রচলিত আছে। স্থানীয় কৃষকদিগের বিশ্বাস যে, ডাঃ হার্ডকালের বিবরণ ও তাঁহার দেহের ক্ষত এই প্রবাদকে বাস্তবে পরিণত করিয়াছে। উক্ত ঘটনা। সম্পর্কে ইহার অধিক কিছু মন্তব্য করা সম্ভব নয়। বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ইহার সমর্থন আদৌ সম্ভবপর বলিয়া আমরা মনে করি না।
কুরিয়ার পত্রিকা এই মন্তব্যটি প্রকাশ করার আগে একবার আমার সঙ্গে আলাপ করলে বুদ্ধিমানের কাজ করত। আমি অনেক ভেবে ঘটনাটার একটা বৈজ্ঞানিক কারণ অনুমান করে এর অবিশ্বাস্যতা খানিকটা দূর করেছি। অন্তত আমার নিজের অভিজ্ঞতার একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি হিসাবে আমি এখানে সেটা পেশ করছি।
আমার মতে (যে মত আমি ঘটনাটা ঘটবার আগেই ডায়েরিতে ইঙ্গিত করেছি) ইংল্যান্ডের এই সব অঞ্চলে ভূগর্ভে বিস্তীর্ণ জলাশয় রয়েছে। পাহাড়ের ফাটল দিয়ে বাইরের জলস্রোত ভিতরে ঢুকেই এইসব জলাশয়ের সৃষ্টি করেছে। জলাশয় থাকলেই বাষ্পের উদ্ভব হয়, এবং বাষ্প থেকে বৃষ্টি ও বৃষ্টি থেকে উদ্ভিদের জন্ম সম্ভব। পৃথিবীর আদি যুগে হয়তো বা এই ভূগর্ভ জগতের সঙ্গে বাইরের জগতের একটা যোগাযোগ ছিল, এবং সেই অবস্থায় হয়তো বাইরের জগতের গাছপালার কিছু বীজ ও তার সঙ্গে কোনও কোনও প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী এই ভূগর্ভজগতে এসে পড়েছিল। এইসব প্রাণীদেরই একটির বংশধর হয়তো এই জানোয়ারকে দেখে মনে হয় আদিম ভাল্লুকের এক বর্ধিত সংস্করণ। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে হয়তো এই ভূগর্ভজগৎ আমাদের পরিচিত জগতের পাশাপাশি একই সঙ্গে অবস্থান করেছে। রোমান সুড়ঙ্গটি খোঁড়ার সময় হয়তো এই ভূগর্ভজগতের কোনও প্রাণী বাইরের জগতের সন্ধান পায়। অন্ধকারবাসী অন্য সব প্রাণীর মতোই এও দৃষ্টিশক্তিহীন জীব। অথচ অন্য সব ইন্দ্রিয় এতই সজাগ যে, চোখের অভাব পূরণ হয়ে যায়। না হলে সে ভেড়ার সন্ধান পাবে কী করে? এরা যে কেবল অন্ধকার রাত্রে চলাফেরা করে, তার কারণ বোধহয়, মণির অভাবে আলো সহ্য হয় না। আমার লণ্ঠনই হয়তো চরম সংকটের মুহূর্তে আমার প্রাণরক্ষা করেছিল। অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। এসব তথ্য আমি লিখে গেলাম আপনাদের বিবেচনার জন্য। একে সমর্থন করা সম্ভব কিনা তা আপনারা বিচার করে দেখবেন। যদি মনে হয় সবটাই অবিশ্বাস্য, তা হলেও আমার কিছু বলার নেই। মূল ঘটনা আপনাদের বিশ্বাস-অবিশ্বাসের অনেক উর্ধ্বে। আর আমার ব্যক্তিগত মতামতের প্রশ্ন যদি তোলেন, তা হলে বলব যে, তারও আর বিশেষ কোনও মূল্য নেই, কারণ আমার কাজ ফুরিয়ে এল।
ডাক্তার জে হার্ডকালের ডায়রির শেষ এখানেই।
দি টেরর অফ ব্লু জন গ্যাপ
সন্দেশ, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪
মঙ্গলই স্বর্গ
মহাকাশ থেকে রকেটটা নেমে আসছে তার গন্তব্যস্থলের দিকে। এতদিন সেটা ছিল তারায় ভরা নিঃশব্দ নিকষ কালো মহাশুন্যে একটি বেগবান ধাতব উজ্জ্বলতা। অগ্নিগর্ভ রকেটটা নতুন। এর দেহ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে উত্তাপ। এর কক্ষের মধ্যে আছে মানুষ ক্যাপ্টেন সমেত সতেরোজন। ওহাইয়ো থেকে রকেটটা যখন আকাশে ওঠে, তখন অগণিত দর্শক হাত নাড়িয়ে এদের শুভযাত্রা কামনা করেছিল। প্রচণ্ড অগ্নদগারের সঙ্গে সঙ্গে রকেটটা সোজা উঠে ছুটে গিয়েছিল মহাশূন্যের দিকে। মঙ্গল গ্রহকে লক্ষ্য করে এই নিয়ে তৃতীয়বার রকেট অভিযান।
এখন রকেট মঙ্গল গ্রহের বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করেছে। তার গতি ক্রমশ কমে আসছে। এই মন্থর অবস্থাতেও তার শক্তির পরিচয় সে বহন করছে। এই শক্তিই তাকে চালিত করেছে মহাকাশের কৃষ্ণসাগরে। চাঁদ পোনোর পরেই তাকে পড়তে হয়েছিল অসীম শূন্যতার মধ্যে। যাত্রীরা নানান প্রতিকূল অবস্থায় বিধ্বস্ত হয়ে আবার সুস্থ হয়ে উঠেছিল। একজনের মৃত্যু হয়। বাকি ষোলোজন এখন স্বচ্ছ জানলার ভিতর দিয়ে বিমুগ্ধ চোখে মঙ্গলের এগিয়ে আসা দেখছে।
মঙ্গল গ্রহ! সোল্লাসে ঘোষণা করল রকেটচালক ডেভিড লাস্টিগ।
এসে গেল মঙ্গল বলল প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যামুয়েল হিংস্টন।
যাক! স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন ক্যাপ্টেন জন ব্ল্যাক।
রকেটটা একটা মসৃণ সবুজ ঘাসে ঢাকা লনের উপর এসে নামল। যাত্রীরা লক্ষ করল, ঘাসের উপর দাঁড়ানো একটি লোহার হরিণের মূর্তি। তারও বেশ কিছুটা পিছনে দেখা যাচ্ছে রোদে ঝলমল একটা বাড়ি, যেটা ভিক্টোরীয় যুগের পৃথিবীর বাড়ির কথা মনে করিয়ে দেয়। সর্বাঙ্গে বিচিত্র কারুকার্য, জানলায় হলদে নীল সবুজ গোলাপি কাচ। বাড়ির বারান্দার সামনে দেখা যাচ্ছে জেরেনিয়াম গাছ আর বারান্দায় মৃদু বাতাসে আপনিই দুলছে ছাত থেকে ঝোলানো একটি দোলনা। বাড়ির চুড়োয় রয়েছে জানলা সমেত একটি গোল ঘর, যার ছাতটা যেন একটা গাধার টুপি।
রকেটের চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে মঙ্গলের এই শান্ত শহর, যার উপর বসন্ত ঋতুর প্রভাব স্পষ্ট। আরও বাড়ি চোখে পড়ে, কোনওটা সাদা, কোনওটা লাল,–আর দেখা যায় লম্বা এম্ মেপ ও হর্স চেস্টনাট গাছের সারি। গিজাও রয়েছে দু-একটা, যার সোনালি ঘণ্টাগুলো এখন নীরব।
রকেটের মানুষগুলি এ দৃশ্য দেখল। তারপর তারা পরস্পরের দিকে চেয়ে আবার বাইরে দৃষ্টি দিল। তারা সকলেই এ-ওর হাত ধরে আছে, সকলেই নির্বাক, শ্বাস নিতেও যেন ভরসা পাচ্ছে না তারা।
এ কী তাজ্জব ব্যাপার! ফিসফিসিয়ে বলল লাস্টিগ।
এ হতে পারে না! বলল স্যামুয়েল হিংস্টন।
হে ঈশ্বর! বললেন ক্যাপ্টেন জন ব্ল্যাক। রাসায়নিক তাঁর গবেষণাগার থেকে স্পিকারে একটি তথ্য ঘোষণা করলেন–বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন আছে। শ্বাস নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।
লাস্টিগ বলল, তা হলে আমরা বেরোই।
দাঁড়াও, দাঁড়াও, বললেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক, আগে তো ব্যাপারটা বুঝতে হবে।
ব্যাপারটা হল এটি একটি ছোট্ট শহর, যাতে মানুষের শাসের পক্ষে যথেষ্ট অক্সিজেন আছে–ব্যস।
প্রত্নতাত্ত্বিক হিংস্টন বললেন, আর এই শহর একেবারে পৃথিবীর শহরের মতো। এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার, কিন্তু তাও সম্ভব হয়েছে।
ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক হিংস্টনের দিকে চেয়ে বললেন, তুমি কি বিশ্বাস করো যে, দুটি বিভিন্ন গ্রহে সভ্যতা ও সংস্কৃতি ঠিক একই সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে গড়ে উঠতে পারে?
সেটা সম্ভব বলে আমার জানা ছিল না।
ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক বাইরের শহরের দিকে চেয়ে বললেন, তোমাদের বলছি শোনো,–জেরেনিয়াম হচ্ছে এমন একটি গাছ, যার অস্তিত্ব পৃথিবীতে পঞ্চাশ বছর আগেও ছিল না। ভেবে দেখো, কত হাজার বছর লাগে একটি উদ্ভিদের আবির্ভাব হতে! এবার তা হলে বলো এটা যুক্তিসম্মত কিনা যে, আমরা মঙ্গল গ্রহে এসে দেখতে পাব–এক, রঙিন কাঁচ বসানো জানলা; দুই, বাড়ির মাথায় গোল ঘরের উপর গাধার টুপি; তিন, বারান্দার ছাত থেকে ঝুলন্ত দোলনা চার, একটি বাদ্যযন্ত্র, যেটা। পিয়ানো ছাড়া আর কিছু হতে পারে না আর পাঁচ–যদি তোমার এই দূরবিনের মধ্যে দিয়ে দেখো তা হলে দেখবে পিয়ানোর উপর একটি গানের স্বরলিপি রয়েছে, যার নাম বিউটিফুল ওহাইয়ো। তার মানে কি মঙ্গলেও একটি নদী আছে, যার নাম ওহাইয়ো?
কিন্তু ক্যাপ্টেন উইলিয়াস কি এর জন্য দায়ী হতে পারেন না?
তার মানে?
ক্যাপ্টেন উইলিয়ামস্ ও তাঁর তিন সহযাত্রী! অথবা ন্যাথেনিয়াল ইয়র্ক ও তাঁর সহযাত্রী। এটা নিঃসন্দেহে এঁদেরই কীর্তি।
এই বিশ্বাস যুক্তিহীন, বললেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক। আমরা যতদূর জানি ইয়র্কের রকেট মঙ্গলে পৌঁছনোমাত্র ধ্বংস হয়। ফলে ইয়র্ক ও তাঁর সহযাত্রীর মৃত্যু হয়। উইলিয়ামসের রকেট মঙ্গল গ্রহে পোঁছনোর পরের দিন ধ্বংস হয়। অন্তত দ্বিতীয় দিনের পর থেকে তাঁদের সঙ্গে পৃথিবীর রেডিও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। উইলিয়ামসের দল যদি বেঁচে থাকত, তা হলে তারা নিশ্চয়ই পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ করত। ইয়র্ক মঙ্গলে এসেছিল এক বছর আগে, আর উইলিয়ামস্ গত অগস্ট মাসে। ধরো যদি তারা এখনও বেঁচে থাকে, এবং মঙ্গল গ্রহে অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাণী বাস করে, তা হলেও কি তাদের পক্ষে এই ক মাসের মধ্যে এমন একটা শহর গড়ে তোলা সম্ভব? শুধু গড়ে তোলা নয়,–সেই শহরের উপর কৃত্রিম উপায়ে বয়সের ছাপ ফেলা সম্ভব? শহরটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এটা অন্তত বছর সত্তরের পুরনো। ওই বাড়ির বারান্দার কাঠের থামগুলো দেখো। গাছগুলোর বয়স একশো বছরের কম হওয়া অসম্ভব। না–এটা ইয়র্ক বা উইলিয়ামসের কীর্তি হতে পারে না। এর রহস্যের চাবিকাঠি খুঁজতে হবে অন্য জায়গায়। আমার কাছে ব্যাপারটা অত্যন্ত গোলমেলে বলে মনে হচ্ছে। এই শহরের অস্তিত্বের কারণ না জানা পর্যন্ত আমি এই রকেট থেকে বেরোচ্ছি না।
লাস্টিগ বলল, এটা ভুললে চলবে না যে, ইয়র্ক ও উইলিয়াস নেমেছিল মঙ্গলের উলটোপিঠে। আমরা ইচ্ছে করেই এ পিঠ বেছে নিয়েছি।
ঠিক কথা, বললেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক। হিংস্র মঙ্গলবাসীদের হাতে যদি ইয়র্ক ও উইলিয়ামসের দলের মৃত্যু হয়ে থাকে, তাই আমাদের বলা হয়েছিল ল্যান্ডিং-এর জন্য অন্য জায়গা বেছে নিতে, যাতে আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়। তাই আমরা নেমেছি এমন একটি জায়গায়, যার সঙ্গে ইয়র্ক বা উইলিয়ামসের কোনও পরিচয়ই হয়নি।
হিংস্টন বলল, যাই হোক, আমি আপনার অনুমতি নিয়ে শহরটা একবার ঘুরে দেখতে চাই। এমনও হতে পারে যে, দুই গ্রহ ঠিক একই সঙ্গে একই নিয়মের মধ্যে গড়ে উঠেছে। একই সৌরজগতের গ্রহে হয়তো এটা সম্ভব। হয়তো আমরা এক যুগান্তকারী আবিষ্কারের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি।
আমার মতে আর একটুক্ষণ অপেক্ষা করা উচিত। হয়তো এই আশ্চর্য ঘটনাই সর্বপ্রথম ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ করবে।
ঈশ্বরের বিশ্বাসের জন্য এমন একটা ঘটনার কোনও প্রয়োজন হয় না, হিংস্টন।
আমি নিজেও ঈশ্বরে বিশ্বাসী, বলল হিংস্টন, কিন্তু এমন একটা শহর ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত গড়ে উঠতে পারে না। শহরের প্রতিটি খুঁটিনাটি লক্ষ করুন। আমি তো সব কি কাঁদব বুঝতে পারছি না।
আসল রহস্যটা কী, সেটা জানার আগে হাসি কান্না কোনওটারই প্রয়োজন নেই।
লাস্টিগ এবার মুখ খুলল।
রহস্য? দিব্যি মনোরম একটি শহর, তাতে আবার রহস্য কী? আমার তো নিজের জন্মস্থানের কথা মনে পড়ছে।
তুমি কবে জন্মেছিলে লাস্টিগ? ব্ল্যাক প্রশ্ন করলেন।
১৯৫০ সালে, স্যার।
আর তুমি, হিংস্টন?
১৯৫৫। আমার জন্ম আইওয়ার গ্রিনেল শহরে। এই শহরটাকে দেখে মনে হচ্ছে আমি আমার জন্মস্থানে ফিরে এসেছি।
তোমাদের দুজনেরই বাপের বয়সী আমি, বললেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক। আমার বয়স আশি। ইলিনয়ে ১৯২০ সালে আমার জন্ম। বিজ্ঞানের দৌলতে গত পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধদের নবযৌবন দান করার উপায় আবিষ্কার হয়েছে। তার জোরেই আমি আজ মঙ্গল গ্রহে আসতে পেরেছি, এবং এখনও ক্লান্তি বোধ করছি না। কিন্তু আমার মনে সন্দেহের মাত্রা তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি। এই শান্ত শহরের চেহারার সঙ্গে ইলিনয়ের গ্রিন ক্লাফ শহরের এত বেশি মিল যে, আমি অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছি। এত মিল স্বাভাবিক নয়।
কথাটা বলে ব্ল্যাক রেডিও অপারেটরের দিকে চাইলেন।
শোনো–পৃথিবীতে খবর পাঠাও। বলল যে, আমরা মঙ্গল গ্রহে ল্যান্ড করেছি। এইটুকু বললেই হবে। বলল, কালকে বিস্তারিত খবর পাঠাব।
তাই বলছি স্যার।
ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক এখনও চেয়ে আছেন শহরটার দিকে। তাঁর চেহারা দেখলে তাঁর আসল বয়সের অর্ধেক বলে মনে হয়। এবার তিনি বললেন, তা হলে যেটা করা যেতে পারে, সেটা হচ্ছে। এইলাস্টিগ, হিংস্টন আর আমি একবার নেমে ঘুরে দেখে আসি। অন্যেরা রকেটেই থাকুক; যদি প্রয়োজন হয়, তখন তারা বেরোতে পারে। কোনও গোলমাল দেখলে তারা এর পরে যে রকেটটা আসার কথা আছে, সেটাকে সাবধান করে দিতে পারে। এর পর ক্যাপ্টেন ওয়াইলডারের আসার কথা। আগামী ডিসেম্বরে রওনা হবেন। যদি মঙ্গল গ্রহে সত্যিই অমঙ্গল কিছু থাকে, তা হলে তাদের সে বিষয়ে তৈরি হয়ে আসতে হবে।
আমরাও তো সে ব্যাপারে তৈরিই আছি। আমাদের তো অস্ত্রের অভাব নেই।
তা হলে সকলে অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত থাকুক।–চলো, আমরা নেমে পড়ি।
তিনজন পুরুষ রকেটের দরজা খুলে নীচে নেমে গেল।
দিনটা চমৎকার। তার উপর আবার বসন্তকালের সব লক্ষণই বর্তমান। একটি রবিন পাখি ফুলে ভরা আপেল গাছের ডালে বসে আনমনে গান গাইছে। মৃদুমন্দ বাতাসে ফুলের পাপড়ি মাঝে মাঝে ঝরে পড়ছে মাটিতে। ফুলের গন্ধও ভেসে আসছে সেই সঙ্গে। কোথা থেকে যেন পিয়ানোর মৃদু টুং-টাং শোনা যাচ্ছে, আর সেইসঙ্গে অন্য কোনও বাড়ি থেকে ভেসে আসছে সেই আদ্যিকালের চোঙাওয়ালা গ্রামোফোনে বাজানো আদ্যিকালের প্রিয় গাইয়ে হ্যারি লডারের গান।
তিনজন কিছুক্ষণ রকেটের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর তারা হাঁটতে শুরু করল খুব সাবধানে, কারণ বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ পৃথিবীর চেয়ে কিছু কম, তাই বেশি পরিশ্রম করা চলবে না।
এবারে গ্রামোফোনের রেকর্ড বদলে গেছে। এবার বাজছে, ও, গিভ মি দ্য জুন নাইট।
লাস্টিগের স্নায়ু চঞ্চল। হিংস্টনেরও তাই। পরিবেশ শান্ত। দূরে কোথা থেকে যেন একটা জলের কুল কুল শব্দ আসছে, আর সেইসঙ্গে একটা ঘোড়ায় টানা ওয়াগনের অতি পরিচিত ঘড় ঘড় শব্দ।
হিংস্টন বলল, স্যার, আমার এখন মনে হচ্ছে, মঙ্গল গ্রহে মানুষ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই আসতে আরম্ভ করেছে।
অসম্ভব!
কিন্তু তা হলে এইসব ঘরবাড়ি, এই লোহার হরিণ মূর্তি, এই পিয়ানো, পুরনো রেকর্ডের গান–এগুলোর অর্থ করবেন কী করে? হিংস্টন ক্যাপ্টেনের হাত ধরে গভীর আগ্রহের সঙ্গে তার মুখের দিকে চাইল। ধরুন যদি এমন হয় যে, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে কিছু যুদ্ধবিরোধী লোক একজোট হয়ে বৈজ্ঞানিকের সাহায্যে একটা রকেট বানিয়ে এখানে চলে আসে?
সেটা হতেই পারে না, হিংস্টন।
কেন হবে না? তখনকার দিনে পৃথিবীতে ঢাক না পিটিয়ে গোপনে কাজ করার অনেক বেশি সুযোগ ছিল।
কিন্তু রকেট জিনিসটা তো আর মুখের কথা নয়! সেটা নিয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করা তখনকার দিনেও অসম্ভব হত।
তারা এখানেই এসে বসবাস শুরু করে, হিংস্টন বলে চলল, এবং যেহেতু তাদের রুচি, তাদের সংস্কৃতি তারা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, তাই তাদের বসবাসের পরিবেশও তৈরি করে নিয়েছিল পৃথিবীর মতো করেই।
তুমি বলতে চাও, তারাই এতদিন এখানে বসবাস করছে?
হ্যাঁ, এবং পরম শান্তিতে। হয়তো তারা আরও বার কয়েক পৃথিবীতে ফিরে গিয়েছিল আরও লোকজন সঙ্গে করে আনার জন্য। একটা ছোট শহরে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে, এমন সংখ্যক লোক এনে তারা যাতায়াত বন্ধ করে দিয়েছিল। পৃথিবীর লোকে তাদের কীর্তি জেনে ফেলে এটা নিশ্চয়ই তারা চায়নি। এই কারণেই এই শহরের চেহারা এত প্রাচীন। এ শহর ১৯২৭-এর পর আর এক দিনও এগিয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। তাই নয় কি? অথবা এমনও হতে পারে যে, মহাকাশ অভিযান ব্যাপারটা আমরা যা মনে করছি, তার চেয়ে অনেক বেশি প্রাচীন। হয়তো পৃথিবীর কোনও একটা অংশে কয়েকজনের চেষ্টায় এটার সূত্রপাত হয়েছিল। তাদের লোক হয়তো মাঝে মাঝে পৃথিবীতে ফিরে গেছে।
তোমার যুক্তি বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠছে।
হতেই হবে স্যার। প্রমাণ আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে। এখন শুধু দরকার এখানকার কিছু লোকের সাক্ষাৎ পাওয়া।
পুরু ঘাসের জন্য তিনজনের হাঁটার শব্দ শোনা যাচ্ছিল না। ঘাসের গন্ধ তাজা। ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের মনে যতই সন্দেহ থাকুক না কেন, একটা পরম শান্তির ভাব তাঁর দেহ-মন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ত্রিশ বছর পরে তিনি এমন একটা শহরে এলেন। মৌমাছির মৃদু গুঞ্জন তাঁর মনে একটা প্রসন্নতা এনে দিয়েছিল। আর পরিবেশের সুস্থ সবলতা তাঁর আত্মাকে পরিতুষ্ট করছিল।
তিনজনেই বাড়িটার সামনের বারান্দায় গিয়ে উঠল। দরজার দিকে এগোনোর সময়ে কাঠের মেঝেতে ভারী বুটের শব্দ হল। ভিতরের ঘরটা এখন দেখা যাচ্ছে। একটা পুঁতির পরদা ঝুলছে। উপরে একটা ঝাড়লণ্ঠন। দেওয়ালে ঝুলছে ঊনবিংশ শতাব্দীর এক জনপ্রিয় শিল্পীর আঁকা একটা বাঁধানো ছবি। ছবির নীচে একটা চেনা ঢঙের আরাম কেদারা। শব্দও শোনা যাচ্ছে–জাগের জলের বরফের টুং টাং। ভিতরের রান্নাঘরে কে যেন পানীয় প্রস্তুত করছে। সেইসঙ্গে নারীকণ্ঠে গুনগুন করে গাওয়া একটি গানের সুর।
ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক কলিং বেল টিপলেন।
ঘরের মেঝের উপর দিয়ে হালকা পায়ের শব্দ এগিয়ে এল। একটি বছর চল্লিশেকের মহিলা–যাঁর পরমে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের পোশাক–পরদা ফাঁক করে তিনজন পুরুষের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিলেন।
আপনারা?
কিছু মনে করবেন না। ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের কণ্ঠস্বরে অপ্রস্তুত ভাব–আমরা,–মানে এ ব্যাপারে আপনি কোনও সাহায্য করতে পারেন কিনা…
ভদ্রমহিলা অবাক দৃষ্টিতে দেখলেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের দিকে।
আপনারা কি কিছু বিক্রিটিক্রি করতে এসেছেন?
না–না! ইয়ে…এই শহরের নামটা যদি–
তার মানে? মহিলার ভ কুঞ্চিত। এখানে এসেছেন আপনারা, অথচ এই শহরের নাম জানেন?
ক্যাপ্টেন বেশ বেকায়দায় পড়ছেন তা বোঝাই যাচ্ছে। বললেন, আসলে আমরা এখানে আগন্তুক। আমরা জানতে চাইছি, এ শহর এখানে এল কী করে, আর আপনারাই বা কী করে এসেছেন?
আপনারা কি সেন্সাস নিতে বেরিয়েছেন?
আজ্ঞে না।
এখানে সবাই জানে যে, এ শহর তৈরি হয়েছিল ১৮৬৮ সালে। আপনারা কি ইচ্ছা করে বোকা সাজছেন?
না–না–মোটেই না, ব্যস্তভাবে বললেন ক্যাপ্টেন, আসলে আমরা আসছি পৃথিবী থেকে।
পৃথিবী?
আজ্ঞে হ্যাঁ। পৃথিবী। সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ। রকেটে করে এসেছি আমরা। আমাদের লক্ষ্যই ছিল চতুর্থ গ্রহ মঙ্গল।
মহিলা যেন কতগুলি শিশুকে বোঝাচ্ছেন, এইভাবে উত্তর দিলেন, এই শহর হল ইলিনয়ে। নাম গ্রিন ব্ল্যাক। আমরা থাকি যে মহাদেশে, তার নাম আমেরিকা। তাকে ঘিরে আছে অতলান্তিক আর প্রশান্ত মহাসাগর। আমাদের গ্রহের নাম পৃথিবী। আপনারা এখন আসতে পারেন। গুডবাই।
ভদ্রমহিলা বাড়ির ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।
তিনজন হতভম্বভাবে পরস্পরের দিকে চাইল।
লাস্টিগ বলল, চলুন, সোজা ভিতরে গিয়ে ঢুকি।
সে হয় না। এটা প্রাইভেট প্রপার্টি। কিন্তু কী আপদ রে বাবা!
তিনজন বারান্দার সিঁড়িতে বসল।
ব্ল্যাক বললেন, এমন একটা কথা কি তোমাদের মনে হয়েছে যে, আমরা হয়তো ভুল পথে আবার পৃথিবীতেই ফিরে এসেছি?
সেটা কী করে সম্ভব? বলল লাস্টিগ।
জানি না! তা জানি না! মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবার শক্তি দাও। হে ভগবান!
হিংস্টন বলল, আমরা সমস্ত রাস্তা হিসাব করে এসেছি। আমাদের ক্রোনোমিটার প্রতি মুহূর্তে বলে দিয়েছে, আমরা কতদূর অগ্রসর হচ্ছি। চাঁদ পেরিয়ে আমরা মহাকাশে প্রবেশ করি। এটা মঙ্গল গ্রহ হতে বাধ্য।
লাস্টিগ বলল, ধরো যদি দৈবদুর্বিপাকে আমাদের সময়ের গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছে–আমরা ত্রিশ চল্লিশ বছর আগের পৃথিবীতে ফিরে এসেছি?
তোমার বকবকানি বন্ধ করো তো লাস্টিগ! অসহিষ্ণুভাবে বললেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক।
লাস্টিগ উঠে গিয়ে আবার কলিং বেল টিপল। ভদ্রমহিলার পুনরাবির্ভাব হতে সে প্রশ্ন করল, এটা কোন সাল?
এটা যে উনিশশো ছাব্বিশ, সেটাও জানেন না?
ভদ্রমহিলা ফিরে গিয়ে একটা দোলনা-চেয়ারে বসে লেমনেড খেতে শুরু করলেন।
শুনলেন তো? লাস্টিগ ফিরে এসে বলল। উনিশশো ছাব্বিশ। আমরা সময়ে পিছিয়ে গেছি। এটা পৃথিবী।
লাস্টিগ বসে পড়ল। তিনজনেরই মনে এখন গভীর উদ্বেগ। হাঁটুর উপর রাখা তাদের হাতগুলো আর স্থির থাকছে না। ক্যাপ্টেন বললেন, এমন একটা অবস্থায় পড়তে হবে, সেটা কি আমরা ভেবেছিলাম? এ কী ভয়াবহ পরিস্থিতি! এমন হয় কী করে? আমাদের সঙ্গে আইনস্টাইন থাকলে হয়তো এর একটা কিনারা করতে পারতেন!
হিংস্টন বলল, আমাদের কথা এখানে কে বিশ্বাস করবে? শেষকালে কী অবস্থায় পড়তে হবে কে জানে! তার চেয়ে ফিরে গেলে হয় না?
না। অন্তত আর একটা বাড়িতে অনুসন্ধান করার আগে নয়।
তিনজনে আবার রওনা দিয়ে তিনটে বাড়ির পরে ওক গাছের তলায় একটা ছোট্ট বাড়ির সামনে দাঁড়াল।
রহস্যের সন্ধান যুক্তিসম্মত ভাবেই হবে, বললেন, ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক, কিন্তু সে যুক্তির নাগাল আমরা এখনও পাইনি। আচ্ছা, হিংস্টন ধরা যাক তুমি যেটা বলেছিলে, সেটাই ঠিক; অর্থাৎ মহাকাশ ভ্রমণ বহুঁকাল আগেই শুরু হয়েছে, ধরা যাক পৃথিবীর লোকে এখানে এসে থাকার কিছুদিন পরেই তাদের নিজেদের এহের জন্য তাদের মন ছটফট করতে শুরু করেছিল। সেটা ক্রমে অসহ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই অবস্থায় একজন মনোবিজ্ঞানী হলে তুমি কী করতে?
হিংস্টন কিছুক্ষণ ভেবে বললে, আমি মঙ্গল গ্রহের জীবনযাত্রাকে ক্রমে বদলিয়ে পৃথিবীর মতন। করে আনতাম। যদি এক গ্রহের গাছপালা নদ-নদী মাঠ-ঘাটকে অন্য আর-এক গ্রহের মতো রূপ দেওয়া সম্ভব হত, তা হলে আমি তাই করতাম। তারপর শহরের সমস্ত লোককে একজোটে হিপনোসিসের সাহায্যে বুঝিয়ে দিতাম যে, তারা যেখানে রয়েছে সেটা আসলে পৃথিবী, মঙ্গল গ্রহ নয়।
ঠিক বলেছ হিংস্টন। এটাই যুক্তিসম্মত কথা। ওই মহিলার ধারণা, তিনি পৃথিবীতেই রয়েছেন। এই বিশ্বাসে তিনি নিশ্চিন্ত। ওঁর মতো এই শহরের প্রত্যেকটি অধিবাসী এক বিরাট মোহে আচ্ছন্ন হয়ে ভ্রান্ত বিশ্বাসে দিন কাটাচ্ছে।
আমি এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত। বলল লাস্টিগ।
আমিও। বলল হিংস্টন।
ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। যাক, এতক্ষণে কিছুটা সোয়াস্তি বোধ করছি। রহস্যের একটা কিনারা হল। সময়ে এগিয়ে। পেছিয়ে যাওয়ার ধারণাটা আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। কিন্তু এইভাবে ভাবতে বেশ ভাল লাগছে।ক্যাপ্টেনের মুখে হাসি ফুটে উঠল। আমার তো মনে হচ্ছে, এবার আমরা নিশ্চিন্তে এদের কাছে আত্মপ্রকাশ করতে পারি।
তাই কি? বলল লাগি। ধরুন যদি এরা এখানে এসে থাকে পৃথিবী থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে। আমরা পৃথিবীর তোক জানলে এরা খুশি নাও হতে পারে।
আমাদের অস্ত্রের শক্তি অনেক বেশি। চলো দেখি, সামনের বাড়ির লোকে কী বলে?
কিন্তু মাঠটা পেয়োনোর আগেই লাস্টিগের দৃষ্টি হঠাৎ রুখে গেল সামনের রাস্তার একটা অংশে।
স্যার–
কী হল লাস্টিগ?
স্যার, এ কী দেখছি চোখের সামনে। লাস্টিগের দৃষ্টি উদ্ভাসিত, তার চোখে জল। সে যেন তার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তাকে দেখে মনে হচ্ছে, সে এই মুহূর্তেই আনন্দের আতিশয্যে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে। সে বেসামাল ভাবে হোঁচট খেতে খেতে রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল।
কোথায় যাচ্ছ তুমি? ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক সঙ্গে সঙ্গে তার পশ্চাদ্ধাবন করলেন।
লাস্টিগ দৌড়ে গিয়ে একটা বাড়ির বারান্দায় উঠে পড়ল। বাড়ির ছাতে একটা লোহার মোরগ।
তারপর শুরু হল দরজায় ধাক্কার সঙ্গে চিৎকার। হিংস্টন ও ক্যাপ্টেন ততক্ষণে তার কাছে পৌঁছে গেছে। দুজনেই ক্লান্ত।
দাদু! দিদিমা! দিদিমা! চেঁচিয়ে চলেছে লাস্টিগ।
বারান্দার দরজার মুখে এসে দাঁড়ালেন এক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা। তাঁরা দুজনেই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন–ডেভিড। তারপর তাঁরা এগিয়ে এসে জড়িয়ে ধরলেন লাস্টিকে।
ডেভিড! কত বড় হয়ে গেছিস তুই! ওঃ, কতদিন পরে দেখছি তোকে! তুই কেমন আছিস?
ডেভিড লাস্টিগ কান্নায় ভেঙে পড়েছে। দাদু! দিদিমা! তোমরা তো দিব্যি আছে। বার বার বুড়োবুড়িকে জড়িয়ে ধরেও যেন লাস্টিগের আশ মেটে না। বাইরে সূর্যের আলো, মন-মাতানো হাওয়া, সব মিলিয়ে পরিপূর্ণ আনন্দের ছবি।
ভেতরে আয়! বরফ দেওয়া চা আছে–অফুরন্ত।
আমার দুই বন্ধু সঙ্গে আছে দিদিমা। লাস্টিগ দুজনের দিকে ফিরে বলল, উঠে আসুন আপনারা।
এসো ভাই এসো, বললেন বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা। ভিতরে এসো। ডেভিডের বন্ধু মানে তো আমাদেরও বন্ধু। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?
বৈঠকখানাটা দিব্যি আরামের। ঘরের এক কোণে একটা গ্র্যান্ডফাদার ক্লক চলছে টিক টিক করে, চারিদিকে সোফার উপর নরম তাকিয়া, দেওয়ালের সামনে আলমারিতে বইয়ের সারি, মেঝেতে গোলাপের নকশায় ভরা পশমের গালিচা। সকলের হাতেই এখন গেলাসের বরফ-চা তাদের তৃষ্ণা উপশম করছে।
তোমাদের মঙ্গল হোক। বৃদ্ধা তাঁর হাতের গেলাসটা ঠোঁটে ঠেকালেন।
তোমরা এখানে কদিন আছ? লাস্টিগ প্রশ্ন করল।
আমাদের মৃত্যুর পর থেকেই। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে বললেন মহিলা।
কীসের পর থেকে? ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের হাতের গেলাস টেবিলে নেমে গেছে।
ওঁরা মারা গেছেন প্রায় ত্রিশ বছর হল, বলল লাস্টিগ।
আর সে কথাটা তুমি অম্লানবদনে উচ্চারণ করলে? ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক চেঁচিয়ে উঠলেন।
বৃদ্ধা উজ্জ্বল হাসি হেসে চাইলেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের দিকে, তাঁর দৃষ্টিতে মৃদু ভর্ৎসনা। কখন কী ঘটে, তা কে বলতে পারে বলে। এই তো আমরা রয়েছি এখানে। জীবনই বা কী আর মৃত্যুই বা কী, তা কে বলবে? আমরা শুধু জানি যে, আমরা আবার বেঁচে উঠেছি। বলতে পারো আমাদের একটা দ্বিতীয় সুযোগ দেওয়া হয়েছে।
বৃদ্ধা উঠে গিয়ে ক্যাপ্টেনের সামনে তাঁর ডান হাতটা এগিয়ে দিলেন। ধরে দেখো। ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক বৃদ্ধার কবজির উপর হাত রাখলেন।
এটা যে রক্তমাংসের হাত, তাতে কোনও সন্দেহ আছে কী?
বাধ্য হয়েই ব্ল্যাককে মাথা নেড়ে স্বীকার করতে হল যে নেই।
তাই যদি হয়, বৃদ্ধা বেশ জোরের সঙ্গে বললেন, তা হলে আর সন্দেহ কেন?
আসল ব্যাপারটা হচ্ছে কি, মঙ্গল গ্রহে এসে এমন একটা ঘটনা ঘটবে, সেটা আমরা ভাবতেই পারিনি।
কিন্তু এখন তো আর সন্দেহের কোনও কারণ নেই, বললেন মহিলা। আমার বিশ্বাস প্রত্যেক গ্রহেই ভগবানের লীলার নানান নিদর্শন রয়েছে।
এই জায়গাকে কি তা হলে স্বর্গ বলা চলে? হিংস্টন প্রশ্ন করল।
মোটেই না। এটা একটা গ্রহ এবং এখানে আমাদের দ্বিতীয়বার বাঁচার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। সেটা কেন দেওয়া হয়েছে, তা কেউ আমাদের বলেনি। কিন্তু তাতে কী এসে গেল? পৃথিবীতেই বা কেন আমরা ছিলাম তার কারণ তো কেউ বলেনি। আমি অবিশ্যি সেই অন্য পৃথিবীর কথা বলছি–যেখান থেকে তোমরা এসেছ। সেটার আগেও যে আর একটা পৃথিবীতে আমরা ছিলাম না, তার প্রমাণ কোথায়?
তা বটে। বললেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক।
লাস্টিগ এখনও হাসিমুখে চেয়ে রয়েছে তার দাদু-দিদিমার দিকে। তোমাদের দেখে যে কী ভাল লাগছে!
ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক উঠে পড়লেন।
এবার তা হলে আমাদের যেতে হয়। আপনাদের আতিথেয়তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।
আবার আসবে তো? বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা একসঙ্গে প্রশ্ন করলেন। রাত্রের খাওয়াটা এখানেই হোক না?
দেখি, চেষ্টা করব। কাজ রয়েছে অনেক। আমার লোকেরা রকেটে রয়েছে, আর
ক্যাপ্টেনের কথা থেমে গেল। তাঁর অবাক দৃষ্টি বাইরের দরজার দিকে। দূর থেকে সমবেত কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। অনেকে সোল্লাসে কাদের যেন স্বাগত জানাচ্ছে।
ব্ল্যাক দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। দূরে রকেটটা দেখা যাচ্ছে। দরজা খোলা, ভিতরের লোক সব বাইরে বেরিয়ে এসেছে। সবাই হাত নাড়ছে আনন্দে। রকেটটাকে ঘিরে মানুষের ভিড়, আর তাদের মধ্য দিয়ে ব্যস্তভাবে ঘোরাফেরা করছে রকেটের তেরোজন যাত্রী। জনতার উপর দিয়ে যে একটা ফুর্তির ঢেউ বয়ে চলেছে, সেটা বোঝাই যাচ্ছে।
এরই মধ্যে একটা ব্যান্ড বাজতে শুরু করল। তার সঙ্গে ছোট ছোট মেয়েদের সোনালি চুল দুলিয়ে নাচ, হুররে! হুররে! ছোট ঘোট ছেলেরা চেঁচিয়ে উঠল। বুড়োরা এ-ওকে চুরুট বিলি করে তাদের মনের আনন্দ প্রকাশ করল।
এরই মধ্যে মেয়র সাহেব একটি বক্তৃতা দিলেন। তার পর রকেটের তেরোজন প্রত্যেকে তাদের খুঁজে-পাওয়া আত্মীয়-স্বজনকে সঙ্গে নিয়ে তাদের বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিল।
ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক আর থাকতে পারলেন না। সমস্ত শব্দ ছাপিয়ে তাঁর চিৎকার শোনা গেল, কোথায় যাচ্ছ তোমরা?
ব্যান্ডবাদকেরাও চলে গেল। এখন আর রকেটের পাশে লোক নেই, সেটা ঝলমলে রোদে পরিত্যক্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।
দেখেছ কাণ্ড, বললেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক। রকেটটাকে ছেড়ে চলে গেল! ওদের ছাল-চামড়া তুলে নেব আমি। আমার হুকুম অগ্রাহ্য করে
স্যর, ওদের মাফ করে দিন, বলল লাস্টিগ। এত পুরনো চেনা লোকের দেখা পেয়েছে ওরা।
ওটা কোনও অজুহাত নয়!
কিন্তু জানলা দিয়ে বাইরে চেনা লোক দেখলে তখন ওদের মনের অবস্থাটা কল্পনা করুন!
কিন্তু তাই বলে হুকুম মানবে না?
এই অবস্থায় আপনার নিজের মনের অবস্থা কী হত সেটাও ভেবে দেখুন!
আমি কখনই হুকুম অগ্রাহ্য–
ক্যাপ্টেনের কথা শেষ হল না। বাইরে রাস্তার ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে আসছে একটি দীর্ঘাঙ্গ যুবক, বছর পঁচিশ বয়স, তার অস্বাভাবিক রকম নীল চোখ দুটো হাসিতে উজ্জ্বল।
জন! যুবকটি এবার দৌড়ে এল ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের দিকে।
এ কী ব্যাপার। ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের যেন স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে।
জন! তুই ব্যাটা এখানে হাজির হয়েছিস?
যুবকটি ক্যাপ্টেনের হাত চেপে ধরে তার পিঠে একটা চাপড় মারল।
তুই! অবাক কণ্ঠে প্রশ্ন এল ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের মুখ থেকে।
তোর এখনও সন্দেহ হচ্ছে?
এডওয়ার্ড! ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক এবার লাস্টিগ ও হিংস্টনের দিকে ফিরলেন, আগন্তুকের হাত তাঁর হাতের মুঠোর মধ্যে।
এ হল আমার ছোট ভাই এডওয়ার্ড। এড–ইনি হলেন হিংস্টন, আর ইনি লাস্টিগ।
দুই ভাইয়ে কিছুক্ষণ হাত ধরে টানাটানির পর সেটা আলিঙ্গনে পরিণত হল।
এড!
জন–হতচ্ছাড়া, তোকে যে আবার কোনও দিন দেখতে পাব–! তুই তো দিব্যি আছিস, এড। কিন্তু ব্যাপারটা কী বল তো? তোর যখন ছাব্বিশ বছর বয়স, তখন তোর মৃত্যু হয়। আমার বয়স তখন উনিশ। কত কাল আগের কথা–আর আজ…
মা অপেক্ষা করছেন, হাসিমুখে বলল এডওয়ার্ড ব্ল্যাক।
মা!
বাবাও!
বাবা! ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক যেন মাথায় প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছেন। তাঁর গতি টলায়মান।–মাবাবা বেঁচে আছেন? কোথায়?
আমাদের সেই পুরনো বাড়ি। ওক নোল অ্যাভিনিউ!
সেই পুরনো বাড়ি। ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের দৃষ্টি উদ্ভাসিত।
শুনলে তোমরা? হিংস্টন ও লাস্টিগের দিকে ফিরলেন জন ব্ল্যাক। কিন্তু হিংস্টন আর নেই। সে তার নিজের ছেলেবেলার বাসস্থানের দেখা পেয়ে সেই দিকে ছুটে গেছে। লাস্টিগ হেসে বলল, এইবার বুঝেছেন ক্যাপ্টেন–আমাদের বন্ধুদের আচরণের কারণটা? হুকুম মানার অবস্থা ওদের ছিল না।
বুঝেছি, বুঝেছি! জন ব্ল্যাক চোখ বন্ধ করে বললেন। যখন চোখ খুলব তখন কি আবার দেখব তুই আর নেই? জন চোখ খুললেন। না তো! তুই তো এখনও আছিস। আর কী খোলতাই হয়েছে তোর চেহারা।
আয়, লাঞ্চের সময় হয়েছে। আমি মাকে বলে রেখেছি।
লাস্টিগ বলল, স্যর, আমি আমার দাদু ও দিদিমার কাছে থাকব। প্রয়োজন হলে খবর দেবেন।
অ্যাঁ? ও, আচ্ছা, ঠিক আছে। পরে দেখা হবে।
এডওয়ার্ড জনের হাত ধরে এগিয়ে গেল একটা বাড়ির দিকে।–মনে পড়ছে বাড়িটা?
আরেব্বাস! আয় তো দেখি, কে আগে পৌঁছতে পারে!
দুজনে দৌড়ল। চারপাশের গাছ, পায়ের নীচের মাটি দ্রুত পিছিয়ে পড়ল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এডওয়ার্ডেরই জয় হল। বাড়িটা ঝড়ের মতো এগিয়ে এসেছে সামনে। –পারলি না, দেখলি তো! বলল এডওয়ার্ড। আমার যে বয়স হয়ে গেছে রে, বলল জন। তবে এটা মনে আছে যে কোনও দিনই তোর সঙ্গে দৌড়ে পারিনি।
দরজার মুখে মা, স্নেহময়ী মা, সেই দোহারা গড়ন। মুখে উজ্জ্বল হাসি। তাঁর পিছনে বাবা, চুলে ছাই রঙের ছোপ, হাতে পাইপ।
মা! বাবা!
শিশুর মতো হাত বাড়িয়ে সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে এগিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন জন ব্ল্যাক।
দুপুরটা কাটল চমৎকার। খাওয়ার পর জন তাঁর রকেট, অভিযানের গল্প করলেন আর সবাই সেটা উপভোগ করলেন। জন দেখলেন যে তাঁর মা একটুও বদলাননি, আর বাবাও ঠিক আগের। মতো করেই দাঁত দিয়ে চুরুটের ডগা ছিঁড়ে কুঞ্চিত করে দেশলাই সংযোগ করছেন। রাত্রে টার্কির মাংস ছিল। টার্কির পা থেকে মাংসের শেষ কণাটুকু চিবিয়ে খেয়ে ক্যাপ্টেন জন পরম তৃপ্তি অনুভব করলেন। বাইরে গাছপালায় আকাশে মেঘে রাত্রির রঙ, ঘরের মধ্যে ল্যাম্পগুলোকে ঘিরে গোলাপি আভা। পাড়ায় আরও অন্য শব্দ শোনা যাচ্ছে–গানের শব্দ, পিয়ানোর শব্দ, দরজা-জানালা খোলা ও বন্ধ করার শব্দ।
মা গ্রামোফোনে একটা রেকর্ড চাপিয়ে নতুন করে ফিরে পাওয়া ছেলের সঙ্গে একটু নাচলেন। মার গায়ে সেই সেন্টের গন্ধ। এ গন্ধ সে দিনও ছিল, যে দিন ট্রেন দুর্ঘটনায় বাপ-মা দুজনেরই একসঙ্গে মৃত্যু হয়। জন যে মা-কে জড়িয়ে ধরে নাচছে, সেটা যে খাঁটি–সেটা জন বেশ বুঝতে পারছে। মা নাচতে নাচতেই বললেন, ব তো জন, দ্বিতীয়বার জীবনধারণের সুযোগ কজনের আসে?
কাল সকালে ঘুম ভাঙবে, আক্ষেপের সুরে বলল জন, তার কিছু পরেই রকেটে করে আমাদের এই স্বর্গরাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হবে।
ও রকম ভেবো না, বললেন মা। কোনও অভিযোগ রেখো না মনে। ঈশ্বর যা করেন, মঙ্গলের জন্য। আমরা তাতেই সুখী।
ঠিক বলেছ, মা।
রেকর্ডটা শেষ হল।
তুমি আজ ক্লান্ত, জনের দিকে পাইপ দেখিয়ে বললেন বাবা। তোমার শোবার ঘর তো রয়েইছে, তোমার পিতলের খাটও রয়েছে।
কিন্তু আগে আমার দলের লোকদের খোঁজ নিতে হবে তো।
কেন?
কেন মানে…ইয়ে, বিশেষ কোনও কারণ নেই। সত্যিই তো। ওরাও হয়তো দিব্যি খাওয়া-দাওয়া করে শুয়ে পড়েছে। একটা রাত ভাল করে ঘুমিয়ে নিলে ওদের বরং লাভই হবে।
গুড নাইট জন, মা তার ছেলের গালে চুমু দিয়ে বললেন। তোমাকে পেয়ে আজ আমাদের কত আনন্দ।
আমারও মন আনন্দে ভরে গেছে।
চুরুট আর সেন্টের গন্ধে ভরা ঘর ছেড়ে জন ব্ল্যাক সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে শুরু করল, তার পিছনে এডওয়ার্ড। দুজনে কথায় মশগুল। দোতলায় পৌঁছে এডওয়ার্ড একটা ঘরের দরজা খুলে দিল। জন দেখল তার পিতলের খাট, দেয়ালে টাঙানো তার স্কুল কলেজের নানা রকম চিহ্ন, সেই সময়কার একটা অতিপরিচিত র্যাকুনের লোমের কোট, যাতে হাত না বুলিয়ে পারল না জন। এ যেন বাড়াবাড়ি, বললেন জন। সত্যি, আমার আর অনুভবের শক্তি নেই। দুদিন সমানে বৃষ্টিতে ভিজলে শরীরের যা অবস্থা হয়, আমার মনটা তেমনই সপসপে হয়ে আছে অজস্র বিচিত্র অনুভূতিতে।
এডওয়ার্ড তার নিজের বিছানায় ও বালিশে দুটো চাপড় মেরে জানালার কাচটা উপরে তুলে দিতে জ্যাসমিন ফুলের গন্ধে ঘরটা ভরে গেল। বাইরে চাঁদের আলো। দূরে কাদের বাড়িতে যেন নাচ-গান হচ্ছে।
তা হলে এটাই হল মঙ্গল গ্রহ, তাঁর পোশাক ছাড়তে ছাড়তে বললেন জন ব্ল্যাক।
এডওয়ার্ডও শোবার জন্য তৈরি হচ্ছে। শার্ট খুলে ফেলতেই তার সুঠাম শরীরটা বেরিয়ে পড়ল।
এখন ঘরের বাতি নেবানো হয়ে গেছে। দুজন পাশাপাশি শুয়ে আছে বিছানায়। কত বছর পরে আবার এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে। ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের মন নানান চিন্তায় ভরপুর।
হঠাৎ তাঁর ম্যারিলিনের কথা মনে হল।
ম্যারিলিন কি এখানে?
জানলা দিয়ে আসা চাঁদের আলোয় শোওয়া এডওয়ার্ড কয়েক মুহূর্ত সময় নিয়ে উত্তরটা দিল।
সে এখানেই থাকে, তবে এখন শহরের বাইরে। কাল সকালেই ফিরবে।
ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক চোখ বন্ধ করে প্রায় আপনমনেই বললেন, ম্যারিলিনের সঙ্গে একটিবার দেখা হলে বেশ হত।
ঘরটায় এখন কেবল দুজনের নিশ্বাসের শব্দ।
গুড নাইট, এড।
সামান্য বিরতির পর উত্তর এল, গুড নাইট, জন।
জন ব্ল্যাক নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে ভাবতে লাগলেন।
এখন দেহ-মনে আর অবসাদ নেই, মাথাও পরিষ্কার। এতক্ষণ নানান পরস্পরবিরোধী অনুভূতি তাকে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে দিচ্ছিল না। কিন্তু এখন…।
প্রশ্ন হচ্ছে–কীভাবে এটা সম্ভব হল? এবং এর কারণ কী? শুধুই কি ভগবানের লীলা! ভগবান কি তাঁর সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এত চিন্তা করেন?
হিংস্টন ও লাস্টিগের কথাগুলো তাঁর মনে পড়ল। নানান যুক্তি, নানান কারণ তাঁর মনের অন্ধকারে আলেয়ার আলোর মতো জেগে উঠতে লাগল। মা। বাবা। এডওয়ার্ড। মঙ্গল। পৃথিবী। মঙ্গলগ্রহের অধিবাসী…
হাজার বছর আগে কারা এখানে বাস করত? তারা কি মঙ্গলগ্রহের প্রাণী, নাকি এদেরই মতো পৃথিবীতে মরে যাওয়া সব মানুষ!
মঙ্গলগ্রহের প্রাণী। কথাটা দুবার মৃদুস্বরে উচ্চারণ করলেন জন ব্ল্যাক।
হঠাৎ তাঁর চিন্তা এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত হল। সব কিছুর একটা মানে হঠাৎ তাঁর মনে জেগে উঠেছে। রক্ত হিমকরা মানে। অবিশ্যি সেটা বিশ্বাস করার কোনও যুক্তি নেই, কারণ ব্যাপারটা অসম্ভব। নিছক আজগুবি কল্পনা মাত্র। ভুলে যাও, ভুলে যাও…মন থেকে দূর করে দাও।
কিন্তু তবু তাঁর মন বলল–একবার তলিয়ে দেখা যাক না ব্যাপারটা। ধরা যাক যে, এরা মঙ্গলগ্রহেরই অধিবাসী। ওরা আমাদের রকেটকে নামতে দেখেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ওদের মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়েছে। ধরা যাক, এরা তৎক্ষণাৎ স্থির করেছে এই পৃথিবীবাসীদের ধ্বংস করতে হবে। কিন্তু ঠিক সোজাসুজি নয়, একটু বাঁকা ভাবে। যেন তাতে একটু চালাকি থাকে, শয়তানি থাকে; যাতে সেটা পৃথিবীর প্রাণীদের কাছে আসে অপ্রত্যাশিতভাবে, আচমকা। এক্ষেত্রে আণবিক মারণাস্ত্রের অধিকারী মানুষের বিরুদ্ধে এরা কী অস্ত্র প্রয়োগ করতে পারে?
এ প্রশ্নেরও উত্তর আছে। টেলিপ্যাথির অস্ত্র, সম্মোহনের অস্ত্র, কল্পনাশক্তির অস্ত্র।
এমন যদি হয় যে, এই সব গাছপালা বাড়িঘর, এই পিতলের খাট–আসলে এর কোনওটাই বাস্তব নয়, সবই আমার কল্পনাপ্রসূত, যে কল্পনার উপর কর্তৃত্ব করছে টেলিপ্যাথি ও সম্মোহনী শক্তির অধিকারী এই মঙ্গলবাসীরা হয়তো এই বাড়ির চেহারা অন্য রকম, যেমন বাড়ি শুধু মঙ্গল গ্রহেই হয়, কিন্তু এদের টেলিপ্যাথি এবং হিপনোসিসের কৌশলে আমাদের চোখে এর চেহারা হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীরই একটি ছোট পুরনো শহরের বাড়ির মতো। ফলে আমাদের মনে একটা প্রসন্নভাব এসে যাচ্ছে আপনা থেকেই। তার উপর নিজেদের হারানো বাবা-মা ভাইবোনকে পেলে কার না মন আনন্দে ভরে যায়?
এই শহরের বয়স আমি ছাড়া আমাদের দলের সকলের চেয়ে বেশি। আমার যখন ছ বছর বয়স তখন আমি ঠিক এই রকম শহর দেখেছি, এই রকম গানবাজনা শুনেছি, ঘরের ভিতর ঠিক এইরকম আসবাব, এই ঘড়ি, এই কাপেট দেখেছি। এমন যদি হয় যে, এই দুর্ধর্ষ চতুর মঙ্গলবাসীরা আমারই স্মৃতির উপর নির্ভর করে ঠিক আমারই মনের মতো একটি শহরের চেহারা আমাদের সামনে উপস্থিত করেছে। শৈশবের স্মৃতিই সবচেয়ে উজ্জ্বল, এমন কথা শোনা যায়। আমার স্মৃতির শহরকে বাস্তব রূপ দিয়ে তারপর তারা আমার রকেটের অন্য যাত্রীদের স্মৃতি থেকেও তাদের মৃত প্রিয়জনদের এই শহরের বাসিন্দা করে দিয়েছে।
ধরা যাক পাশের ঘরে যে বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা শুয়ে আছেন, তাঁরা আসলে মোটেই আমার মা বাবা নন। আসলে তাঁরা ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন দুই মঙ্গলগ্রহবাসী, যারা আমার মনে তাঁদের ইচ্ছামতো ধারণা আরোপ করতে সক্ষম।
আর রকেটকে ঘিরে আজকের ওই আমোদ ও ব্যান্ড-বাদ্য? কী আশ্চর্য বুদ্ধি কাজ করছে ওর পিছনে যদি সত্যিই এটা টেলিপ্যাথি হয়। প্রথমে লাস্টিগকে হাত করা গেল,তার পর হিংস্টনকে, তার পর রকেটের বাকি সব যাত্রীদের ঘিরে ফেলা হল গত বিশ বছরের মধ্যে হারানো তাদের আত্মীয় ও প্রিয়জনদের দিয়ে, যাতে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমার হুকুম অগ্রাহ্য করে। রকেট ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। এর চেয়ে স্বাভাবিক আর কী হতে পারে? এখানে মনে সন্দেহ প্রবেশ করার সুযোগ কোথায়? তাই তো এখন দলের সকলেই শুয়ে আছে বিভিন্ন বাড়িতে, বিভিন্ন খাটে, নিরস্ত্র অবস্থায়; আর রকেটটাও খালি পড়ে আছে চাঁদনি রাতে। কী ভয়াবহ হবে সেই উপলব্ধি, যদি সত্যিই জানা যায় যে, এই সমস্ত ঘটনার পিছনে রয়েছে আমাদের সকলকে হত্যা করার অভিসন্ধি। হয়তো মাঝরাত্রে আমার পাশের খাটে আমার ভাইয়ের চেহারা বদলে গিয়ে হয়ে যাবে ভয়ঙ্কর একটা কিছু–যেমন চেহারা সব মঙ্গলবাসীরই হয়। আর সেইসঙ্গে অন্য পনেরোটা বাড়িতে আমার দলের লোকদের প্রিয়জনদেরও চেহারা যাবে পালটে, আর তারা শুরু করবে ঘুমন্ত পৃথিবীবাসীদের সংহার…
চাদরের তলায় ক্যাপ্টেন জনের হাত দুটো আর স্থির থাকছে না। আর তাঁর সমস্ত শরীর হয়ে গেছে বরফের মতোঠাণ্ডা। যা এতক্ষণ ছিল কল্পনা, তা এখন বাস্তব রূপ ধরে তাঁর মনে গভীর। আতঙ্কের সঞ্চার করছে।
ধীরে ধীরে ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক বিছানায় উঠে বসলেন। রাত এখন নিস্তব্ধ। বাজনা থেমে গেছে। বাইরে বাতাসের শব্দও আর নেই। পাশের খাটে ভাই শুয়ে ঘুমোচ্ছে।
অতি সন্তর্পণে গায়ের চাদরটা গুটিয়ে পাশে রাখলেন ক্যাপ্টেন ব্ল্যাক। তারপর খাট থেকে নেমে কোনও শব্দ না করে ঘরের দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই ভাইয়ের কণ্ঠস্বরে থমকে দাঁড়ালেন।
কোথায় যাচ্ছ দাদা?
কী বললে?
এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছ?
জল খেতে যাচ্ছিলাম।
কিন্তু তোমার তো তেষ্টা পায়নি।
হ্যাঁ, পেয়েছে।
আমি জানি পায়নি।
ক্যাপ্টেন জন পালাবার চেষ্টায় দৌড়ে গেলেন দরজার দিকে। কিন্তু দরজা পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেন না।
পরদিন সকালে মঙ্গলবাসীদের ব্যান্ডে শোনা গেল করুণ সুর। শহরের অনেক বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল লম্বা লম্বা কাঠের বাক্স বহনকারীর দল। মৃত ব্যক্তিদের বাপ-মা-ভাই-বোন সকলের চোখেই জল, তারা চলেছে গিজার দিকে, যেখানে মাটিতে ষোলোটি নতুন গর্ত খোঁড়া হয়েছে।
মেয়র আর একটি বক্তৃতা দিলেন এবার দুঃখ প্রকাশ করার জন্য, যদিও তাঁকে আজ চিনতে পারা মুশকিল, কারণ তাঁর চেহারা দ্রুত রূপান্তরিত হচ্ছে। যেমন হচ্ছে এই শহরের সমস্ত প্রাণীই। ক্যাপ্টেন ব্ল্যাকের মা, বাবা ও ভাইয়ের চোখে জল হলেও তাদের চেহারা দ্রুত বিকৃত হয়ে আসছে, ফলে তাদের এখন চেনা প্রায় অসম্ভব।
কাঠের কফিনগুলো গর্তের মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হল। কে যেন মন্তব্য করল, রাতারাতি লোকগুলো শেষ হয়ে গেল।
এখন কফিনের ঢাকনার ওপর মঙ্গলের মাটি নিক্ষিপ্ত হচ্ছে।
এই শুভদিনে আজ এখানে সকলের ছুটি।
মারস্ ইজ হেভেন
সন্দেশ, শারদীয়া ১৩৯১
মোল্লা নাসিরুদ্দিনের আরো গল্প
১.
একদিন এক জ্ঞাতি এসে নাসিরুদ্দিনকে একটা হাঁস উপহার দিলে। নাসিরুদ্দিন ভারী খুশি হয়ে সেটার মাংস রান্না করে জ্ঞাতিকে খাওয়ালে।
কয়েকদিন পরে মোল্লাসাহেবের কাছে একজন লোক এসে বললে, আপনাকে যিনি হাঁস দিয়েছিলেন, আমি তাঁর বন্ধু।
নাসিরুদ্দিন তাকেও মাংস খাওয়ালে।
এর পর আরেকদিন আরেকজন এসে বলে, আপনাকে যিনি হাঁস দিয়েছিলেন, আমি তার বন্ধুর বন্ধু। নাসিরুদ্দিন তাকেও খাওয়ালে।
তারপর এল বন্ধুর বন্ধুর বন্ধু। মোল্লাসাহেব তাকেও খাওয়ালে।
এর কিছুদিন পরে আবার দরজায় টোকা পড়ল। আপনি কে?দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলে নাসিরুদ্দিন।
আজ্ঞে মোল্লাসাহেব, যিনি আপনাকে হাঁস দিয়েছিলেন, আমি তার বন্ধুর বন্ধুর বন্ধুর বন্ধু।
ভেতরে আসুন, বললে নাসিরুদ্দিন, খাবার তৈরিই আছে।
অতিথি মাংসের ঝোল দিয়ে পোলাও মেখে একগ্লাস খেয়ে ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কীসের মাংস মোল্লাসাহেব?
হাঁসের বন্ধুর বন্ধুর বন্ধুর বন্ধুর, বললে নাসিরুদ্দিন।
.
২.
নাসিরুদ্দিন বাজারে গিয়ে দেখে সারি সারি খাঁচায় ময়না বিক্রি হচ্ছে, সেগুলির দাম একেকটা পঞ্চাশ টাকা।
পরদিন সে তার ধাড়ি মুরগিটাকে নিয়ে বাজারে হাজির, ভাবছে সেটাকে বিক্রি করে মোটা টাকা পাবে।
যখন দেখল যে পাঁচ টাকার বেশি দাম দিতে চায় না কেউ, তখন সে তম্বি শুরু করলে। তাই দেখে একজন লোক এসে তাকে বললে, মোল্লাসাহেব, কালকের পাখিগুলো যে কথা বলতে পারে, তাই এত দাম। তোমার মুরগি কথা বলে কি?
নাসিরুদ্দিন চোখ রাঙিয়ে বললে, পুঁচকে পাখি বকবক করে কানের পোকা নড়িয়ে দিলে তার হয়ে গেল পঞ্চাশ টাকা দাম, আর আমার এতবড় মুরগি নিজের ভাবনা নিয়ে চুপচাপ থাকে বলে তার কদর নেই? যতসব ইয়ে।
.
৩.
নাসিরুদ্দিন বাজার থেকে খাবার আনে, আর তার গিন্নি সেগুলো লুকিয়ে এক বন্ধুকে দিয়ে দেয়।
ব্যাপার কী বলো তো? একদিন মোল্লা বললে–খাবারগুলো যায় কোথায়?
বেড়ালে চুরি করে, বললেন গিন্নি।
কথাটা শুনেই নাসিরুদ্দিন তার সাধের কুড়ুলটা এনে আলমারির ভিতর লুকিয়ে ফেললে।
ওটা কী হল? জিজ্ঞেস করলেন গিন্নি।
বেড়াল যদি দশ পয়সার খাবার চুরি করতে পারে বললে নাসিরুদ্দিন, তা হলে দশ টাকার কুড়ুলটা বাইরে ফেলে রাখি কোন ভরসায়?
.
৪.
এক সন্ধ্যায় নির্জন রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে নাসিরুদ্দিন কয়েকজন ঘোড়সওয়ারকে এগিয়ে আসতে দেখে প্রমাদ গুনলে। নির্ঘাত এরা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে শাহেন শা-র ফৌজে ভর্তি করে দেবে।
রাস্তার পাশেই গোরস্থান; নাসিরুদ্দিন এক দৌড়ে তাতে ঢুকে ঘাপটি মেরে রইল।
ঘোড়সওয়াররা কৌতূহলী হয়ে গোরস্থানে ঢুকে দেখে নাসিরুদ্দিন একটা কবরের ধারে কাঠ হয়ে পড়ে আছে। এখানে কী হচ্ছে মোল্লাসাহেব? তারা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে।
নাসিরুদ্দিন বুঝলে তার আঁচে গলতি হয়েছে। সে বললে, সব প্রশ্নের তো আর সহজ উত্তর হয় না। যদি বলি যে তোমাদের জন্যই আমার এখানে আসা, আর আমার জন্যই তোমাদের এখানে আসা, তা হলে কিছু বুঝবে?
.
৫.
নাসিরুদ্দিন তার পুরনো বন্ধু জামাল সাহেবের দেখা পেয়ে ভারী খুশি। বললে, বন্ধু, চলো পাড়া বেড়িয়ে আসি।
লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে গেলে আমার এই মামুলি পোশাক চলবে না, বললে জামাল সাহেব। নাসিরুদ্দিন তাকে একটি বাহারের পোশাক ধার দিলে।
প্রথম বাড়িতে গিয়ে নাসিরুদ্দিন গৃহকর্তাকে বললে, ইনি হলেন আমার বিশিষ্ট বন্ধু জামাল সাহেব। এঁর পোশাটা আসলে আমার।
দেখা সেরে বাইরে বেরিয়ে এসে জামাল সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, তোমার কেমনতরো আক্কেল হে! পোশাকটা যে তোমার সেটা কি না বললেই চলত না?
পরের বাড়িতে গিয়ে নাসিরুদ্দিন বললে, জামাল সাহেব আমার পুরনো বন্ধু। ইনি যে পোশাকটা পরেছেন সেটা কিন্তু ওঁর নিজেরই।
জামাল সাহেব আবার খাপ্পা। বাইরে বেরিয়ে এসে বললেন, মিথ্যে কথাটা কে বলতে বলেছিল তোমায়?
কেন? বললে নাসিরুদ্দিন, তুমি যেমন চাইলে তেমনই তো বললাম।
না, বললেন জামালসাহেব, পোশাকের কথাটা না বললেই ভাল।
তিন নম্বর বাড়িতে গিয়ে নাসিরুদ্দিন বললে, আমার পুরনো বন্ধু জামাল সাহেবের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি যে পোশাটা পরেছেন সেটার কথা অবিশ্যি না বলাই ভাল।
.
৬.
নাসিরুদ্দিন নাকি বলে বেড়াচ্ছে যারা নিজেদের বিজ্ঞ বলে তারা আসলে কিচ্ছু জানে না। এই খবর শুনে সাতজন সেরা বিজ্ঞ নাসিরুদ্দিনকে রাজার কাছে ধরে এনে বললে, শাহেন শা, এই ব্যক্তি অতি দুর্জন। ইনি আমাদের বদনাম করে বেড়াচ্ছেন। এর শাস্তির ব্যবস্থা হোক।
রাজা নাসিরুদ্দিনকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কিছু বলার আছে?
আগে কাগজ কলম আনা হোক, জাঁহাপনা, বললে নাসিরুদ্দিন।
কাগজ কলম এল।
এদের সাতজনকে একটি করে দেওয়া হোক।
তাও হল।
এবার সাতজনে আলাদা করে আমার প্রশ্নের জবাব লিখুন। প্রশ্ন হল-রুটির অর্থ কী?
সাত পণ্ডিত উত্তর লিখে রাজার হাতে কাগজ দিয়ে দিলেন, রাজা পর পর উত্তরগুলো পড়ে গেলেন।
পয়লা নম্বর লিখেছেন রুটি একপ্রকার খাদ্য।
দুই নম্বর–ময়দা ও জলের সংমিশ্রণে তৈয়ারি পদার্থকে বলে রুটি।
তিন নম্বর–রুটি ঈশ্বরের দান।
চার নম্বর–একপ্রকার পুষ্টিকর আহার্যকে বলে রুটি।
পাঁচ নম্বর–রুটির অর্থ করতে গেলে আগে জানা দরকার, কোনপ্রকার রুটির কথা বলা হচ্ছে।
ছয় নম্বর–রুটির অর্থ এক মূর্খ ব্যক্তি ছাড়া সকলেই জানে।
সাত নম্বর–রুটির প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার।
উত্তর শুনে নাসিরুদ্দিন বললে, জাঁহাপনা, যে জিনিস এঁরা প্রতিদিন খাচ্ছেন, তার মানে এঁরা সাতজন সাতরকম করলেন, অথচ যে লোককে এঁরা কখনও চোখেই দেখেননি তাকে সকলে একবাক্যে নিন্দে করছেন। এক্ষেত্রে কে বিজ্ঞ কে মূর্খ সেটা আপনিই বিচার করুন।
রাজা নাসিরুদ্দিনকে বেকসুর খালাস দিলেন।
.
৭.
নাসিরুদ্দিনের দজ্জাল গিন্নি ফুটন্ত সুরুয়া এনে কর্তার সামনে রাখল তার জিভ পুড়িয়ে তাকে জব্দ করবে বলে, কিন্তু ভুলে সে নিজেই দিয়ে ফেলেছে তাতে চুমুক। ফলে তার চোখে জল এসে গেছে।
নাসিরুদ্দিন তাই দেখে বলে, হল কী? কাঁদছ নাকি?
গিন্নি বললেন, মা মারা যাবার ঠিক আগে সুরুয়া খেয়েছিলেন, আহা! সেই কথাটা মনে পড়ে গেল।
এবার নাসিরুদ্দিনও সুরুয়ায় চুমুক দিয়েছে, আর তার ফলে তারও চোখ ফেটে জল।
সে কী, তুমিও কাঁদছ নাকি? শুধোলেন গিন্নি।
নাসিরুদ্দিন বললে, তোমায় জ্যান্ত রেখে তোমার মা মারা গেলেন, এটা কি খুব সুখের কথা?
সন্দেশ, পৌষ ১৩৮৪
মোল্লা নাসিরুদ্দিনের আরো গল্প (২)
১.
রাজদরবারে নাসিরুদ্দিনের খুব খাতির।
একদিন খুব খিদের মুখে বেগুন ভাজা খেয়ে ভারী খুশি হয়ে রাজা নাসিরুদ্দিনকে বললেন, বেগুনের মতো এমন সুস্বাদু খাদ্য আর আছে কি?
বেগুনের জবাব নেই, বললে নাসিরুদ্দিন।
রাজা হুকুম দিলেন, এবার থেকে রোজ বেগুন খাব।
তারপর পাঁচদিন দুবেলা বেগুন খেয়ে ছদিনের দিন রাজা হঠাৎ বেঁকে বসলেন। খানসামাকে ডেকে বললেন, দূর করে দে আমার সামনে থেকে এই বেগুন ভাজা।
বেগুন অখাদ্য, সায় দিয়ে বললে নাসিরুদ্দিন।
রাজা একথা শুনে ভারী অবাক হয়ে বললেন, সে কী মোল্লাসাহেব, তুমি যে এই সেদিনই বললে বেগুনের জবাব নেই!
আমি তো আপনার মোসাহেব, জাঁহাপনা, বললে নাসিরুদ্দিন, বেগুনের তো নই।
.
২.
নাসিরুদ্দিন সরাইখানায় ঢুকে গম্ভীরভাবে মন্তব্য করলে, সুর্যের চেয়ে চাঁদের উপকারিতা অনেক বেশি।
কেন মোল্লাসাহেব? অবাক হয়ে প্রশ্ন করলে সবাই।
চাঁদ আলো দেয় রাত্তিরে, বললে নাসিরুদ্দিন, দিনে আলোর দরকারটা কী শুনি?
.
৩.
নাসিরুদ্দিন তার এক বন্ধুকে নিয়ে সরাইখানায় ঢুকেছে দুধ খাবে বলে। পয়সার অভাব, তাই এক গেলাস দুধ দুজন আধাআধি করে খাবে।
বন্ধু বললে, তুমি আগে খেয়ে নাও তোমার অর্ধেক। বাকিটা আমি পরে চিনি দিয়ে খাব।
চিনিটা আগেই দাও না ভাই, বললে নাসিরুদ্দিন, তা হলে দুজনেরই দুধ মিষ্টি হবে।
বন্ধু মাথা নাড়লে। আধ গেলাসের মতো চিনি আছে আমার সঙ্গে, আর নেই।
নাসিরুদ্দিন সরাইখানার মালিকের সঙ্গে দেখা করে খানিকটা নুন নিয়ে এল। ঠিক আছে, সে বললে বন্ধুকে, এই নুন ঢাললাম দুধে। আমি অর্ধেক নোনতা খাব, বাকি অর্ধেক মিষ্টি খেও তুমি।
.
৪.
মোল্লা এক ছোঁকরাকে মাটির কলসি দিয়ে পাঠালে কুয়ো থেকে জল তুলে আনতে। দেখিস, কলসিটা ভাঙিসনি যেন, বলে একটা থাপ্পড় মারলে ছোঁকরার গালে।
এক পথচারী ব্যাপারটা দেখে বললে, কলসি না ভাঙতেই চড়টা মারলেন কেন মোল্লাসাহেব?
তোমার যা বুদ্ধি,বললে নাসিরুদ্দিন, ভাঙার পরে চড় মারলে কি আর কলসি জোড়া লেগে যাবে?
.
৫.
নাসিরুদ্দিন একটা মনিহারী দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, এখানে পেরেক পাওয়া যায়?
আজ্ঞে হ্যাঁ, বললে দোকানদার।
আর চামড়া?
আজ্ঞে হ্যাঁ, যায়।
আর সুতো?
যায়, আজ্ঞে।
আর রঙ?
তাও যায়।
তা হলে তুমি বসে না থেকে একটা জুতো তৈরি করে ফেলো না বাপু!
.
৬.
নাসিরুদ্দিন এক পড়শির কাছে গিয়ে হাত পাতলে। এক গরিব তার দেনা শোধ করতে পারছে না। তার সাহায্যে যদি কিছু দেন।
পড়শির মনটা দরাজ, সে খুশি হয়ে তার হাতে কিছু টাকা দিয়ে বললে, আহা বেচারি! এই ঋণগ্রস্ত অভাগাটি কে, মোল্লাসাহেব?
আমি, বলে নাসিরুদ্দিন হাওয়া।
কিছুদিন পরে নাসিরুদ্দিন আবার সেই পড়শির কাছে এসে হাত পেতেছে। পড়শি একবার ঠকে সেয়ানা হয়ে গেছে। বললে, বুঝেছি। দেনাদারটি এবারও তুমিই তো?
আজ্ঞে না। বিশ্বাস করুন। এবার সত্যিই আমি না।
পড়শির আবার মন ভিজল। নাসিরুদ্দিনের হাতে টাকা দিয়ে বললে, এবার কার দুঃখ দূর করতে যাচ্ছ মোল্লাসাহেব?
আজ্ঞে, আমার।
কীরকম?
আজ্ঞে এই অধম এবার পাওনাদার।
.
৭.
সুসংবাদ দিলে বকশিশ পায় জেনে একজন লোক নাসিরুদ্দিনকে গিয়ে বললে, তোমার জন্য খুব ভাল খবর আছে, মোল্লাসাহেব।
কী খবর?
তোমার পাশের বাড়িতে পোলাও রান্না হচ্ছে।
তাতে আমার কী?
তোমাকে সে পোলাওয়ের ভাগ দেবে বলছে।
তাতে তোমার কী?
.
৮.
নাসিরুদ্দিন নদীর ধারে বসে আছে, এমন সময় দেখে নজন অন্ধ নদী পেরোবার তোড়জোড় করছে।
নাসিরুদ্দিন তাদের কাছে প্রস্তাব করলে যে, জনপিছু এক পয়সা করে নিয়ে সে নজনকে পর পর কাঁধে করে পার করে দেবে। অন্ধরা রাজি হয়ে গেল।
নাসিরুদ্দিন আটজনকে পার করে ননম্বরের বেলায় মাঝনদীতে হোঁচট খেতে পিঠের অন্ধ জলে। তলিয়ে গেল।
বাকি আটজন দেরি দেখে ওপার থেকে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে, কী হল মোল্লাসাহেব?
এক পয়সা বাঁচল তোমাদের, বললে নাসিরুদ্দিন।
.
৯.
নাসিরুদ্দিন আর তার গিন্নি একদিন বাড়ি ফিরে এসে দেখে চোর এসে বাড়ি তছনছ করে দিয়ে গেছে। গিন্নি তো রেগে আগুন। বললে, এ তোমার দোষ। সদর দরজায় তালা দাওনি, তাই এই দশা।
পড়শিরাও সেই একই সুর ধরলে। একজন বললে, জানলাগুলোও তো ভাল করে বন্ধ করোনি দেখছি।
আরেকজন বললে, চোর আসতে পারে সেটা আগেই বোঝা উচিত ছিল।
আরেকজন বললে, দরজার তালাগুলোও পরীক্ষা করে দেখা উচিত।
কী আপদ! বললে নাসিরুদ্দিন, তোমরা দেখছি শুধু আমার পিছনেই লাগতে শুরু করলে!
দোষ তো তোমারই মোল্লাসাহেব, পড়শিরা বললে।
বটে? বললে নাসিরুদ্দিন, আর চোরের বুঝি দোষ নেই?
.
১০.
নাসিরুদ্দিনের ভারী শখ একটা নতুন জোব্বা বানাবে, তাই পয়সা জমিয়ে দরজির দোকানে গেল ফরমাশ দিতে। দরজি মাপ নিয়ে বললে, আল্লা করেন তো এক সপ্তাহ পরে আপনি জোব্বা পেয়ে যাবেন।
নাসিরুদ্দিন এক সপ্তাহ কোনওরকমে ধৈর্য ধরে তারপর আবার গেল দরজির দোকানে।
একটু অসুবিধা ছিল মোল্লাসাহেব, বললে দরজি, আল্লা করেন তো কাল আপনি অবশ্যই জোব্বা পেয়ে যাবেন।
পরদিন গিয়েও হতাশ। মাফ করবেন মোল্লাসাহেব, বললে দরজি, আর একটি দিন আমাকে সময় দিন। আল্লা করেন তো কাল সকালে নিশ্চয় রেডি পাবেন আপনার জোব্বা।
নাসিরুদ্দিন এবার বললে, আল্লা না করে তুমি করলে জোব্বাটা কবে পাব সেটা জানতে পারি কি?
.
১১.
এক প্রবীণ দার্শনিক সরাইখানায় বসে বিলাপ করছেন, বিচিত্র জীব এই মানুষ। কোনও কিছুতেই তৃপ্তি নেই। শীতকালে বলে ঠাণ্ডায় মলাম, গ্রীষ্মে বলে গরমে প্রাণ আইঢাই।
সবাই তার কথায় সায় দিয়ে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল।
বসন্তের বিরুদ্ধে যার নালিশ আছে সে হাত তোলো, বললে নাসিরুদ্দিন।
.
১২.
নাসিরুদ্দিনের গানবাজনা শেখার শখ হয়েছে। এক জবরদস্ত ওস্তাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, আপনি বাদ্যযন্ত্র শেখাতে কত নেন?
প্রথম মাসে তিন রৌপ্যমুদ্রা, তারপর থেকে প্রতি মাসে এক রৌপ্যমুদ্রা।
বেশ, তা হলে দ্বিতীয় মাস থেকেই শুরু করব আমি, বললে নাসিরুদ্দিন।
.
১৩.
এক চোর নাসিরুদ্দিনের বাড়িতে ঢুকে তার প্রায় সর্বস্ব চুরি করে রওনা দিল নিজের বাড়ির দিকে।
নাসিরুদ্দিন রাস্তা থেকে সব দেখে একটি কম্বল কাঁধে নিয়ে চোরের পিছু ধাওয়া করে তার বাড়িতে ঢুকে কম্বল গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল মেঝেতে।
কে হে তুমি? চোর জিজ্ঞেস করলে, আমার বাড়িতে কেন?
আমার জিনিস যখন সবই এখানে, বললে নাসিরুদ্দিন, এখন থেকে এটাই আমার বাড়ি নয় কি?
.
১৪.
সরাইখানায় কজন সৈনিকের আগমন হয়েছে। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের বীরত্বের বড়াই করছে। একজন বললে, খোলা তলোয়ার হাতে এমন তেজের সঙ্গে ছুটলাম আমি দুশমনের দিকে যে-তারা একেবারে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। আমায় রেখে কার সাধ্য!
সবাই একথা শুনে সমস্বরে বাহবা দিলে। নাসিরুদ্দিনও এককালে যুদ্ধ করেছে। সে বললে, তোমার কথা শুনে আমার নিজের একটা যুদ্ধের ঘটনা মনে পড়ছে। এক শত্রুর পা কেটে ফেলেছিলাম তলোয়ারের এক কোপে।
তাই শুনে এক প্রবীণ যোদ্ধা বললে, ওইখানেই তো ভুল। কাটা উচিত ছিল মুণ্ডুটা।
মুণ্ডুটা না থাকলে আর মুণ্ডু কাটব কোত্থেকে? বললে নাসিরুদ্দিন।
.
১৫.
এক পড়শি মোল্লাসাহেবের কাছে একগাছ দড়ি ধার চাইতে এসেছে।
পাবে না বলে নাসিরুদ্দিন।
কেন মোল্লাসাহেব?
দড়ি কাজে লাগছে।
ওটা তো মাটিতে পড়ে আছে আজ কদিন থেকে মোল্লাসাহেব।
ওটাই কাজ।
পড়শি তবু আশা ছাড়ে না। বললে, কদিন চলবে কাজ মোল্লাসাহেব?
যদ্দিন না ওটা ধার দেওয়া দরকার বলে মনে করি বললে নাসিরুদ্দিন।
.
১৬.
নাসিরুদ্দিন হামামে গেছে গোসল করতে। পরিচারক তার ছেঁড়া পোশাক দেখে আধখানা সাবান আর একটা ময়লা তোয়ালে ছুঁড়ে দিলে তার দিকে।
নাসিরুদ্দিন কিন্তু যাবার সময় তাকে ভালরকম বকশিশ দিয়ে গেল। পরিচারক ভাবলে, এ কেমন হল? খাতির না করেই যদি এত পাওয়া যায় তা হলে খাতির করলে না জানি কত মিলবে!
পরের সপ্তাহে নাসিরুদ্দিন আবার গেছে হামামে। এবার তাকে দেখেই পরিচারক একেবারে বাদশার হালে তার তোষামোদ করেছে। আচ্ছা রকম দলাই-মালাই করে, গায়ে আতর ছিটিয়ে দিয়ে, কাজের শেষে হাত পাততেই নাসিরুদ্দিন তাকে একটি তামার পয়সা দিয়ে বললে, গতবারের জন্য এই বকশিশ। এবারেরটা তো আগেই দেওয়া আছে।
.
১৭.
নাসিরুদ্দিন এক আমীরের বাড়ি গেছে দুর্ভিক্ষের চাঁদা তুলতে। দরোয়ানকে বললে, তোমার মনিবকে গিয়ে বলল মোল্লাসাহেব চাঁদা নিতে এসেছেন।
দরোয়ান ভিতরে গিয়ে মিনিটখানেক পরে ফিরে এসে বললে, আজ্ঞে, মনিব একটু বাইরে গেছেন।
তা হলে তোমায় একটা কথা বলে যাই,বললে নাসিরুদ্দিন, তোমার মনিব এলে তাঁকে বোলো যে, বেরোবার সময় তাঁর মুণ্ডুটা যেন জানলার ধারে রেখে না যান। কখন চোর আসে বলা কি যায়!
সন্দেশ, শারদীয়া ১৩৮৫
মোল্লা নাসিরুদ্দিনের গল্প
১.
নাসিরুদ্দিনের বন্ধুরা একদিন তাকে বললে, চলো, আজ রাত্রে আমরা তোমার বাড়িতে খাব।
বেশ, এসো আমার সঙ্গে, বললে নাসিরুদ্দিন।
বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে সে বললে, তোমরা একটু সবুর করো, আমি আগে গিন্নিকে বলে আসি ব্যবস্থা করতে।
গিন্নি তো ব্যাপার শুনে এই মারে তো সেই মারে। বললেন, চালাকি পেয়েছ? এত লোকের রান্না কি চাট্টিখানি কথা? যাও, বলে এসো ওসব হবে-টবে না।
নাসিরুদ্দিন মাথায় হাত দিয়ে বললে, দোহাই গিন্নি, ও আমি বলতে পারব না। এতে আমার ইজ্জত থাকবে না।
তবে তুমি ওপরে গিয়ে ঘরে বসে থাকো। ওরা এলে যা বলার আমি বলব।
এদিকে নাসিরুদ্দিনের বন্ধুরা প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করে শেষটায় তার বাড়ির সামনে এসে হাঁক দিল, ওহে নাসিরুদ্দিন, আমরা এসেছি, দরজা খোলো৷
দরজা ফাঁক হল, আর ভিতর থেকে শোনা গেল গিন্নির গলা।
ও বেরিয়ে গেছে।
বন্ধুরা অবাক! কিন্তু আমরা তো ওকে ভিতরে ঢুকতে দেখলাম। আর সেই থেকে তো আমরা দরজার দিকেই চেয়ে আছি। ওকে তো বেরোতে দেখিনি।
গিন্নি চুপ। বন্ধুরা উত্তরের অপেক্ষা করছে। নাসিরুদ্দিন দোতলার ঘর থেকে সব শুনে আর থাকতে না পেরে বললে, তোমরা তো সদর দরজায় চোখ রেখেছ; সে বুঝি খিড়কি দিয়ে বেরোতে পারে না?
.
২.
নাসিরুদ্দিন তার বাড়ির বাইরে বাগানে কী যেন খুঁজছে। তাই দেখে এক পড়শি জিজ্ঞেস করলে, ও মোল্লাসাহেব, কী হারালে গো?
আমার চাবিটা, বললে নাসিরুদ্দিন।
তাই শুনে লোকটিও বাগানে এসে চাবি খুঁজতে লাগল। কিছুক্ষণ খোঁজার পর সে জিজ্ঞেস করলে, ঠিক কোনখানটায় ফেলেছিলে চাবিটা, মনে পড়ছে?
আমার ঘরে।
সে কী! তা হলে এখানে খুঁজছ কেন?
ঘরটা অন্ধকার, বললে নাসিরুদ্দিন। যেখানে খোঁজার সুবিধে সেইখানেই তো খুঁজব?
.
৩.
নাসিরুদ্দিনের পোষ পাঁঠাটার উপর পড়শিদের ভারী লোভ, কিন্তু নানান ফিকির করেও তারা সেটাকে হাত করতে পারে না। শেষটায় একদিন তারা নাসিরুদ্দিনকে বললে, ও মোল্লাসাহেব, বড় দুঃসংবাদ। কাল নাকি প্রলয় হবে। এই দুনিয়ার সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে।
তা হলে পাঁঠাটাকেও ধ্বংস করা হোক, বললে নাসিরুদ্দিন।
সন্ধেবেলা পড়শিরা দলেবলে এসে দিব্যি ফুর্তিতে পাঁঠার ঝোল খেয়ে গায়ের জামা খুলে নাসিরুদ্দিনের বৈঠকখানায় নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল।
সকালে ঘুম থেকে উঠে তারা দেখে তাদের জামা উধাও।
প্রলয়ই যদি হবে, বললে নাসিরুদ্দিন, তা হলে জামাগুলো আর কোন কাজে লাগবে ভাই? তাই আমি সেগুলোকে আগুনে ধ্বংস করে ফেলেছি।
.
৪.
নাসিরুদ্দিন বাজার থেকে মাংস কিনে এনে তার গিন্নিকে দিয়ে বললে, আজ কাবাব খাব; বেশ ভাল করে রাঁধো দিকি।
গিন্নি রান্নাটান্না করে লোভে পড়ে নিজেই সব মাংস খেয়ে ফেললে। কর্তাকে তত আর সে কথা বলা যায় না, বললে, বেড়াল খেয়ে ফেলেছে।
এক সের মাংস সবটা খেয়ে ফেলল?
সবটা।
বেড়ালটা কাছেই ছিল, নাসিরুদ্দিন সেটাকে দাঁড়িপাল্লায় চড়িয়ে দেখলে ওজন ঠিক এক সের।
এটাই যদি সেই বেড়াল হয়, বললে নাসিরুদ্দিন, তা হলে মাংস কোথায়? আর এটাই যদি সেই মাংস হয়, তা হলে বেড়াল কোথায়?
.
৫.
নাসিরুদ্দিনের যখন বয়স খুব কম তখন একদিন তার বাপ তাকে বললেন, ওরে নসু, এবার থেকে খুব ভোরে উঠিস।
কেন বাবা? অভ্যেসটা ভাল, বললেন নসুর বাপ। আমি সেদিন ভোরে উঠে বেড়াতে গিয়ে রাস্তার মধ্যিখানে পড়ে থাকা এক থলে মোহর পেয়েছি।
সে থলে তো আগের দিন রাত্রেও পড়ে থাকতে পারে, বাবা। সেটা কথা নয়। আর তা ছাড়া আগের দিন রাত্রেও ওই পথ দিয়ে হাঁটছিলুম আমি; তখন কোনও মোহরের থলে ছিল না।
তা হলে ভোরে উঠে লাভ কী বাবা? বললে নাসিরুদ্দিন। যে লোক মোহরের থলি হারিয়েছিল সে নিশ্চয় তোমার চেয়েও বেশি ভোরে উঠেছিল।
.
৬.
শিকারে বেরিয়ে পথে প্রথমেই নাসিরুদ্দিনের সামনে পড়ে রাজামশাই খেপে উঠলেন। লোকটা অপয়া। আজ আমার শিকার পণ্ড। ওকে চাবকে হটিয়ে দাও।
রাজার হুকুম তামিল হল।
কিন্তু শিকার হল জবরদস্ত।
রাজা নাসিরুদ্দিনকে ডেকে পাঠালেন।
কসুর হয়ে গেছে নাসিরুদ্দিন। আমি ভেবেছিলাম তুমি অপয়া। এখন দেখছি তা নয়।
নাসিরুদ্দিন তিন হাত লাফিয়ে উঠল।
আপনি ভেবেছিলেন আমি অপয়া? আমায় দেখে আপনি ছাব্বিশটা হরিণ মারলেন, আর আপনাকে দেখে আমি বিশ ঘা চাবুক খেলাম। অপয়া যে কে, সেটা বুঝতে পারলেন না?
.
৭.
নাসিরুদ্দিন একজন লোককে মুখ ব্যাজার করে রাস্তার ধারে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করলে, তার কী হয়েছে। লোকটা বললে, আমার জীবন বিষময় হয়ে গেছে মোল্লাসাহেব। হাতে কিছু পয়সা ছিল, তাই নিয়ে দেশ ঘুরতে বেরিয়েছি, যদি কোনও সুখের সন্ধান পাই।
লোকটির পাশে তার বোঁচকায় কতগুলো জিনিসপত্র রাখা ছিল। তার কথা শেষ হওয়ামাত্র নাসিরুদ্দিন সেই বোঁচকাটা নিয়ে বেদম বেগে দিলে চম্পট। লোকটাও হাঁ হাঁ করে তার পিছু নিয়েছে, কিন্তু নাসিরুদ্দিনকে ধরে কার সাধ্য! দেখতে দেখতে সে রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলে ঢুকে হাওয়া। এইভাবে লোকটিকে মিনিটখানেক ধোঁকা দিয়ে সে আবার সদর রাস্তায় ফিরে বোঁচকাটাকে রাস্তার মাঝখানে রেখে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইল। এদিকে সেই লোকটিও কিছুক্ষণ পরে এসে হাজির। তাকে এখন আগের চেয়েও দশগুণ বেশি বেজার দেখাচ্ছে। কিন্তু রাস্তায় তার বোঁচকাটা পড়ে আছে দেখেই সে মহাফুর্তিতে একটা চিৎকার দিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।
গাছের আড়াল থেকে নাসিরুদ্দিন বললে, দুঃখীকে সুখের সন্ধান দেবার এও একটা উপায়।
.
৮.
তর্কবাগীশ মশাই নাসিরুদ্দিনের সঙ্গে তর্ক করবেন বলে দিনক্ষণ ঠিক করে তার বাড়িতে এসে দেখেন মোল্লাসাহেব বেরিয়ে গেছেন। মহা বিরক্ত হয়ে তিনি মোল্লার সদর দরজায় খড়ি দিয়ে লিখে গেলেন মূর্খ।
নাসিরুদ্দিন বাড়ি ফিরে এসে কাণ্ড দেখে এক হাত জিভ কেটে এক দৌড়ে তর্কবাগীশ মশাইয়ের বাড়ি গিয়ে তাঁকে বললে, ঘাট হয়েছে পণ্ডিতমশাই, আমি বেমালুম ভুলে গেসলুম আপনি আসবেন। শেষটায় বাড়ি ফিরে দরজায় আপনার নামটা লিখে গেছেন দেখে মনে পড়ল।
.
৯.
গাঁয়ের লোকে একদিন ঠিক করল নাসিরুদ্দিনকে নিয়ে একটু মশকরা করবে। তারা তার কাছে গিয়ে সেলাম ঠুকে বললে, মোল্লাসাহেব, আপনার এত জ্ঞান, একদিন মসজিদে এসে আমাদের তত্ত্বকথা শোনান না! নাসিরুদ্দিন এককথায় রাজি।
দিন ঠিক করে ঘড়ি ধরে মসজিদে হাজির হয়ে নাসিরুদ্দিন উপস্থিত সবাইকে সেলাম জানিয়ে বললে, ভাই সকল, বলো তো দেখি আমি এখন তোমাদের কী বিষয় বলতে যাচ্ছি?
সবাই বলে উঠল, আজ্ঞে সে তো আমরা জানি না।
মোল্লা বলল, এটাও যদি না জানো তা হলে আর আমি কী বলব! যাদের বলব তারা এত অজ্ঞ হলে চলে কী করে?
এই বলে নাসিরুদ্দিন রাগে গজগজ করতে করতে মসজিদ ছেড়ে সোজা বাড়ি চলে এল।
গাঁয়ের লোক নাছোড়বান্দা। তারা আবার তার বাড়িতে গিয়ে হাজির।
আজ্ঞে, আসছে শুক্রবার আপনাকে আর একটিবার আসতেই হবে মসজিদে।
নাসিরুদ্দিন গেল, আর আবার সেই প্রথম দিনের প্রশ্ন দিয়েই শুরু করল। এবার সব লোকে একসঙ্গে বলে উঠল, আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি।
সবাই জেনে ফেলেছ? তা হলে তো আর আমার কিছু বলার নেই,এই বলে নাসিরুদ্দিন আবার বাড়ি ফিরে গেল। গাঁয়ের লোক তবুও ছাড়ে না। পরের শুক্রবার নাসিরুদ্দিন আবার মসজিদে হাজির হয়ে তার সেই বাঁধা প্রশ্ন করল। এবার আর মোল্লাকে রেহাই দেবে না গাঁয়ের লোক, তাই অর্ধেক বলল জানি, অর্ধেক বলল জানি না।
বেশ, তা হলে যারা জানো তারা বলল, আর যারা জানো না তারা শোনো–এই বলে নাসিরুদ্দিন আবার ঘরমুখো হল।
.
১০.
নাসিরুদ্দিন বাড়ির ছাতে কাজ করছে, এমন সময় এক ভিখিরি রাস্তা থেকে হাঁক দিল, মোল্লাসাহেব, একবারটি নীচে আসবেন?
নাসিরুদ্দিন ছাত থেকে রাস্তায় নেমে এল। ভিখিরি বলল, দুটি ভিক্ষে দেবেন মোল্লাসাহেব?
তুমি এই কথাটা বলার জন্য আমায় ছাত থেকে নামালে?
ভিখিরি কাঁচুমাচু হয়ে বললে, মাফ করবেন মোল্লাসাহেব,–গলা ছেড়ে ভিক্ষে চাইতে শরম লাগে।
হুঁ…তা তুমি ছাতে এসো আমার সঙ্গে।
ভিখিরি তিনতলার সিঁড়ি ভেঙে ছাতে ওঠার পর নাসিরুদ্দিন বললে, তুমি এসো হে; ভিক্ষেটিক্ষে হবে না।
.
১১.
নাসিরুদ্দিন লেখাপড়া বেশি জানে না ঠিকই, কিন্তু তার গাঁয়ে এমন লোক আছে যাদের বিদ্যে তার চেয়েও অনেক কম। তাদেরই একজন নাসিরদ্দিনকে দিয়ে নিজের ভাইকে একটা চিঠি লেখালে। লেখা শেষ হলে পর সে বললে, মোল্লাসাহেব কী লিখলেন একবারটি পড়ে দেন, যদি কিছু বাদটাদ গিয়ে থাকে।
নাসিরুদ্দিন প্রিয় ভাই আমার পর্যন্ত পড়ে ঠেকে গিয়ে বললে, পরের কথাটা বাক্স না গরম না ছাগল সেটা বোঝা যাচ্ছে না।
সে কী মোল্লাসাহেব, আপনার লেখা চিঠি আপনিই পড়তে পারেন না তো অপরে পড়বে কী করে?
সেটা আমি কী জানি? বললে নাসিরুদ্দিন। আমায় লিখতে বললে আমি লিখলাম। পড়াটাও কি আমার কাজ নাকি?
লোকটা কিছুক্ষণ ভেবে মাথা নেড়ে বললে, তা ঠিকই বললেন বটে! আর এ চিঠি তো আপনাকে। লেখা নয়, কাজেই আপনি পড়তে না পারলে আর ক্ষতি কী?
হক কথা, বললে নাসিরুদ্দিন।
.
১২.
নাসিরুদ্দিন একবার ভারতবর্ষে এসে এক সাধুর দেখা পেয়ে ভাবলে, আমার মতো জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তির পক্ষে সাধুর সাক্ষাৎ পাওয়া পরম সৌভাগ্য। এর সঙ্গে আলাপ না করলেই নয়!
তাঁকে জিজ্ঞেস করতে সাধু বললেন তিনি একজন যোগী; ঈশ্বরের সৃষ্ট যত প্রাণী আছে সকলের। সেবাই তাঁর ধর্ম।
নাসিরুদ্দিন বললে, ঈশ্বরের সৃষ্টি একটি মৎস্য একবার আমাকে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেছিল।
এ-কথা শুনে যোগী আহ্লাদে আটখানা হয়ে বললেন, আমি এত দীর্ঘকাল প্রাণীর সেবা করেও তাদের এত অন্তরঙ্গ হতে পারিনি। একটি মৎস্য আপনার প্রাণরক্ষা করেছে শুনে এই দেখুন আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে। আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন না তো কে থাকবে?
নাসিরুদ্দিন যোগীর সঙ্গে থেকে তার কাছ থেকে যোগের নানা কসরত শিক্ষা করলে। শেষে একদিন যোগী বললেন, আর ধৈর্য রাখা সম্ভব নয়। অনুগ্রহ করে যদি সেই মৎস্যের উপাখ্যানটি শোনান।
একান্তই শুনবেন?
হে গুরু! বললেন যোগী, শোনার জন্য আমি উদগ্রীব হয়ে আছি।
তবে শুনুন, বললে নাসিরুদ্দিন, একবার খাদ্যাভাবে প্রাণ যায় যায় অবস্থায় আমার বঁড়শিতে একটি মাছ ওঠে। আমি সেটা ভেজে খাই।
.
১৩.
এক ধনীর বাড়িতে ভোজ হবে খবর পেয়ে নাসিরুদ্দিন সেখানে গিয়ে হাজির।
ঘরের মাঝখানে বিশাল টেবিলের উপর লোভনীয় সব খাবার সাজানো রয়েছে রুপোর পাত্রে। টেবিল ঘিরে কুরসি পাতা, তাতে বসেছে হোমরা-চোমরা সব ভাইয়েরা। নাসিরুদ্দিন সেদিকে এগোতেই কর্মকর্তা তার মামুলি পোশাক দেখে তাকে ঘরের এক কোনায় ঠেলে দিলেন। নাসিরুদ্দিন বুঝলে সেখানে খাবার পৌঁছতে হয়ে যাবে রাত কাবার। সে আর সময় নষ্ট না করে সোজা বাড়ি ফিরে গিয়ে তোরঙ্গ থেকে তার ঠাকুরদাদার আমলের একটা ঝলমলে আলখাল্লা আর একটা মণিমুক্তো বসানো আলিশান পাগড়ি বার করে পরে আবার নেমন্তন্ন বাড়িতে ফিরে গেল।
এবার কর্মকর্তা তাকে একেবারে খাস টেবিলে বসিয়ে দিলেন, আর বসামাত্র নাসিরুদ্দিনের সামনে এসে হাজির হল ভুরভুরে খুশবুওয়ালা পোলাওয়ের পাত্র। নাসিরুদ্দিন প্রথমেই পাত্র থেকে খানিকটা পোলাও তুলে নিয়ে তার আলখাল্লায় আর পাগড়িতে মাখিয়ে দিলে। পাশে বসেছিলেন এক আমীর। তিনি ভারী অবাক হয়ে বললেন, জনাব, আপনি খাদ্যদ্রব্য যেভাবে ব্যবহার করছেন তা দেখে আমার কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার অর্থ জানতে পারলে আমি বিশেষ বাধিত হব।
অর্থ, খুবই সোজা, বললে নাসিরুদ্দিন। এই আলখাল্লা আর এই পাগড়ির দৌলতেই আমার সামনে এই ভোজের পাত্র। এদের ভাগ না দিয়ে আমি একা খাব সে কি হয়?
.
১৪.
একদিন রাত্রে দুজনের পায়ের শব্দ পেয়ে নাসিরুদ্দিন ভয়ে একটা আলমারিতে ঢুকে লুকিয়ে রইল।
লোক দুটো ছিল চোর। তারা বাক্সপ্যাঁটরা সবই খুলছে, সেইসঙ্গে আলমারিটাও খুলে দেখে তাতে মোল্লাসাহেব ঘাপটি মেরে আছেন।
কী হল মোল্লাসাহেব, লুকিয়ে কেন?
লজ্জায়, বললে নাসিরুদ্দিন। আমার বাড়িতে তোমাদের নেবার মতো কিছুই নেই তাই লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছি না ভাই।
.
১৫.
এক চাষা নাসিরুদ্দিনের কাছে এসে বললে, বাড়িতে চিঠি দিতে হবে মোল্লাসাহেব। মেহেরবানি করে আপনি যদি লিখে দেন।
নাসিরুদ্দিন মাথা নাড়লে। সে হবে না।
কেন মোল্লাসাহেব?
আমার পায়ে জখম।
তাতে কী হল মোল্লাসাহেব? চাষা অবাক হয়ে বললে, পায়ের সঙ্গে চিঠির কী?
নাসিরুদ্দিন বললে, আমার হাতের লেখা কেউ পড়তে পারে না। তাই চিঠির সঙ্গে আমাকেও যেতে হবে সে চিঠি পড়ে দিতে। জখম পায়ে সেটা হবে কী করে শুনি?
.
১৬.
নাসিরুদ্দিন এক বাড়িতে চাকরের কাজ করছে। মনিব তাকে একদিন ডেকে বললেন, তুমি অযথা সময় নষ্ট করো কেন হে বাপু? তিনটে ডিম আনতে কেউ তিনবার বাজার যায়? এবার থেকে একবারে সব কাজ সেরে আসবে।
একদিন মনিবের অসুখ করেছে, তিনি নাসিরুদ্দিনকে ডেকে বললেন, হাকিম ডাকো।
নাসিরুদ্দিন গেল, কিন্তু ফিরল অনেক দেরিতে, আর সঙ্গে একগুষ্টি লোক নিয়ে।
মনিব বললেন, হাকিম কই?
তিনি আছেন, আর সঙ্গে আরও আছেন, বললে নাসিরুদ্দিন।
আরও কেন?
আজ্ঞে হাকিম যদি বলেন পুলটিশ দিতে, তার জন্য লোক চাই। জল গরম করতে কয়লা লাগবে, কয়লাওয়ালা চাই। আপনার শ্বাস উঠলে পর কোরান পড়ার লোক চাই, আর আপনি মরলে পরে লাশ বইবার লোক চাই।
সন্দেশ, শারদীয়া ১৩৮৪