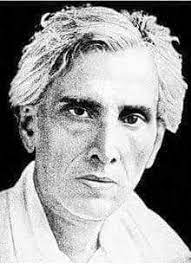- বইয়ের নামঃ পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত (শরৎ)
- লেখকের নামঃ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
- বিভাগসমূহঃ রচনাবলী
অপ্রকাশিত খণ্ডরচনা
এক
১। বিদ্যা বা লেখাপড়া শেখার ফলে Standard of living-এর standard বাড়বেই এবং economic condition ভালো না হলে পারিবারিক অসন্তোষ বাড়বেই।
২। Economic অবস্থা বাড়াবার উপায় একমাত্র শিক্ষিত পুরুষদের industry গড়ে তোলা, ছোট দোকান করবার শিক্ষা ছেলেবেলা থেকে শিখতে হয়। B. A. পাস করার পরে ও জিনিস চলে না, ওখানে অশিক্ষাই বরং কাজের।
১২৬৪
৩। জাতের ছোট-বড় ভাঙ্গার চেষ্টা করতে হবে।
৪। মুষ্টিমেয় সমাজের মধ্যে থেকে মুষ্টিমেয় বাঙালী ভদ্রসন্তানের অপরিসীম sacrifice কাজে লাগে না। এই মুষ্টিমেয় লোকগুলি যদি সমাজের সর্বস্তরের মধ্যে থেকে আসতো, সমস্ত সমাজের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ থাকতো।
৫। Permanent Settlement-এর জন্যেই জমিদার, তালুকদার ও অসংখ্য মধ্যবিত্ত middlemen সমস্ত সমাজের economic অবস্থাকে বাড়তে দেয়নি—কেবলমাত্র জমি আঁকড়ে থেকে শুধু কৃষকেরাই যা-কিছু দেশের wealth সৃষ্টি করছে। বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে Permanent Settlement না থাকার জন্যই ওদেশে industry-র উন্নতি হচ্ছে। জমি কেনা ও বেশী সুদে লগ্নি কারবার করা এই হচ্ছে বাঙালার ধনী হবার একমাত্র পন্থা।
৬। কলেজের মেয়ে,—বই মুখস্থ করে, আর পরীক্ষা পাস করার চেষ্টায় ক্রমাগত রাত্রি জাগরণে শরীর-স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে যায়—আর সব লোকসানই পূরণ হতে পারে কিন্তু যে সন্তান এদের জন্মাবে সে চিররুগ্ন হয়েই থাকবে। (‘বাতায়ন’, ১৬ বৈশাখ, ১৩৪৫)
দুই
১। সহজ বুদ্ধিই দুনিয়ায় সবচেয়ে অ-সহজ।
২। বিশেষ কাজের বিশেষ ধারা পৌনঃপুনিক ব্যবহারে দাঁড়ায় মানুষের অভ্যাসে। সেই ব্যষ্টির অভ্যস্ত কাজ ব্যাপ্ত হয়ে যখন সমষ্টিতে ছড়িয়ে পড়ে তখনই সে হয় আচার।
৩। আমাদের পূর্বপুরুষেরও পূর্বে যাঁরা, তাঁরা চিন্তা এবং বুদ্ধি দিয়ে দেখিয়েছিলেন বহু ক্লেশসাধ্য কাজের পরিণাম মঙ্গলময়।
৪। আচার-বিচার কথাটা এক নিঃশ্বাসেই বলি বটে, কিন্তু আচার জিনিসটা বুদ্ধি দিয়ে প্রবর্তিত হয়নি, তাই যুক্তি দিয়েও এর পরিবর্তন হয় না।
৫। অদৃষ্ট জিনিসটাই চিরদিন জীবনসংগ্রাম ও ধর্মের মাঝে অচ্ছেদ্য ও অফুরন্ত সেতুর শিকলের মতো জুড়ে আছে।
৬। দৃশ্যমান সকল বস্তুরই আরম্ভটা অজ্ঞেয়তত্ত্বে অদৃশ্য হয়েছে।
৭। ধর্মনিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে ধর্মের বই কত পড়তে হয়। সমাজের উন্নতি করতে হলে, সমাজ সম্বন্ধে কত অভিজ্ঞতা দরকার। তার সমস্ত খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করতে নেই। (‘বাতায়ন’, ৬ আশ্বিন, ১৩৪৫)
॥ সমাপ্ত॥
আত্মকথা
“My childhood and youth were passed in great poverty. I received almost no education for want of means. From my father I inherited nothing except, as I believe, his restless spirit and his keen interest in literature. The first made me a tramp and sent me out tramping the whole of India quite early, and the second made me a dreamer all my life. Father was a great scholar, and he had tried his hand at stories and novels, dramas and poems, in short, every branch of literature, but never could finish anything. I have not his work now-somehow it got lost; but I remember poring over those incompleteness. Over again in my childhood, and many a night I kept awake regretting their incompleteness, and thinking what might have been their conclusion if finished. Probably this led to my writing short stories when I was barely seventeen. But I soon gave up the habit as useless, and almost forgot in the long years that followed that I could even write a sentence in my boyhood. A mere accident made me start again, after the lapse of about eighteen years. Some of my old acquaintances started a little magazine, but no one of note would condescend to contribute to it, as it was so small and insignificant. When almost hopeless, some of them suddenly remembered me, and after much persuasion they succeeded in extracting from me a promise to write for it. This was in the year 1913.
I promised most unwillingly-perhaps only to put them off till I had returned to Rangoon and could forget all about it. But sheer volume and force of their letters and telegrams compelled me at last to think seriously about writing again. I sent them a short story for their magazine Jamuna. This became at once extremely popular, and made me famous in one day. Since then I have been writing regularly. In Bengal, perhaps, I am the only fortunate writer who has not had to struggle.”
“আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটেনি। পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকারসূত্রে আর কিছুই পাইনি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করেছিল—আমি অল্প বয়সেই সারা ভারত ঘুরে এলাম। আর পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবন ভরে আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম। আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনটাই তিনি শেষ করতে পারেন নি। তাঁর লেখাগুলি আজ আমার কাছে নেই—কবে কেমন করে হারিয়ে গেছে, সে কথা আজ মনে পড়ে না। কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে, ছোটবেলায় কতবার তাঁর অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। কেন তিনি এগুলি শেষ করে যাননি, এই বলে কত দুঃখই না করেছি। অসমাপ্ত অংশগুলি কি হতে পারে, ভাবতে ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে।
এই কারণেই বোধ হয় সতের বৎসর বয়সের সময় আমি গল্প লিখতে শুরু করি। কিন্তু কিছুদিন বাদে গল্পরচনা অ-কেজোর কাজ মনে করে আমি অভ্যাস ছেড়ে দিলাম। তারপর অনেক বৎসর চলে গেল। আমি যে কোন কালে একটি লাইনও লিখেছি, সে কথা ভুলে গেলাম।
“আঠার বৎসর পরে একদিন লিখতে আরম্ভ করলাম। কারণটা দৈব দুর্ঘটনারই মত। আমার গুটিকয়েক পুরাতন বন্ধু একটি ছোট মাসিকপত্র বের করতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান্ লেখকদের কেউই এই সামান্য পত্রিকায় লেখা দিতে রাজী হলেন না। নিরুপায় হয়ে তাঁদের কেউ কেউ আমাকে স্মরণ করলেন। বিস্তর চেষ্টায় তাঁরা আমার কাছ থেকে লেখা পাঠাবার কথা আদায় করে নিলেন। এটা ১৯১৩ সনের কথা। আমি নিমরাজী হয়েছিলাম। কোন রকমে তাঁদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যেই আমি লেখা দিতেও স্বীকার হয়েছিলাম। উদ্দেশ্য, কোন রকমে একবার রেঙ্গুন পৌঁছতে পারলেই হয়। কিন্তু চিঠির পর চিঠি আর টেলিগ্রামের তাড়া আমাকে অবশেষে সত্য সত্যই আবার কলম ধরতে প্ররোচিত করল। আমি তাঁদের নবপ্রকাশিত ‘যমুনা’র জন্য একটি ছোটগল্প পাঠালাম। এই গল্পটি প্রকাশ হতে না হতেই বাঙ্গালার পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করল। আমিও একদিনেই নাম করে বসলাম। তারপর আমি অদ্যাবধি নিয়মিতভাবে লিখে আসছি। বাঙ্গালাদেশে বোধ হয় আমিই একমাত্র সৌভাগ্যবান লেখক, যাকে কোনদিন বাধার দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়নি।’’**(‘বাতায়ন’, শরৎ স্মৃতি-সংখ্যা, ১৩৪৪)
কানকাটা
গত ফাল্গুনের (১৩১৯) ‘সাহিত্যে’ শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রবাবুর “কানকাটা” ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণীত হইয়াছে। তথ্যটি সত্য কিংবা অসত্য আলোচিত হইবার পূর্বে একটা সন্দেহ স্বতঃই মনে উঠে, ঠাকুরমশাই প্রবন্ধটি হাসাইবার অভিপ্রায়ে লিখেন নাই ত? কেননা, ইহা সত্য সত্যই সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা এবং যথার্থই সত্য, তাহা মনে করিলেও দুঃখ হয়। তবে যদি হাসাইবার অভিপ্রায়ে লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রবন্ধটি নিশ্চয়ই সার্থক হইয়াছে। কিন্তু আর কোন উদ্দেশ্য থাকিলে বোধ করি ব্যর্থ হইয়াছে এবং হওয়াই মঙ্গল। যাহা হউক, উক্ত প্রবন্ধে ঠাকুরমশাই বলিয়াছেন, “কানকাটা, কন্দকাটা, বা উড়িষ্যার খোন্দ জাতিরা বাইবেল-কথিত কানানাইট জাতি ভিন্ন আর কিছুই নয়।” এই ‘কিছুই নয়’টি প্রমাণ করিবার জন্য তিনি এই উভয় জাতির মধ্যে অনেক সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন এবং জাতিতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। আমার এক আত্মীয় সেদিন বলিতেছিলেন, আজকাল বাঙ্গালাদেশে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের লেখক সবাই। কেবল ঝগড়া করিতে চায়—রামের আঁতুর-ঘর পশ্চিমমুখো কিংবা পূবমুখো ছিল। কথাটা তাঁহার নিতান্ত মিথ্যা নয় দেখিতেছি।
কিন্তু, জাতিতত্ত্ব জিনিসটি শুধু যদি খেলনার জিনিস হইত, কিংবা শখ করিয়া খান-দুই এ-ও-তা বই নাড়াচাড়া করিলেই ইহাতে ব্যুৎপত্তি জন্মিত, তাহা হইলে, আমার এ প্রতিবাদের আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু তাহা নহে। ইহা সত্য-উদ্ঘাটন—চুট্কি গল্প লেখা নহে। অতএব, জাতিতত্ত্ববিৎ বলিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া খ্যাতি অর্জন করিবার পূর্বে কিছু ‘সলিড’ পরিশ্রমের আবশ্যক। সুতরাং যে দুর্ভাগারা অনেকদিন ধরিয়া গায়ের অনেক রক্ত জল করিয়া নীরস বইগুলি ঘাঁটিয়া মরিয়াছে, এ ভার তাহাদের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত মনে সরস কবিতা এবং রসাল সাহিত্যিক প্রবন্ধে বা গল্পে মনোনিবেশ করাই বুদ্ধির কাজ। খান-দুই বই ভাসা ভাসা রকম দেখিয়া লইয়া এবং গোটা-দুই সাদৃশ্য উপরে উপরে মিলাইয়া দিয়া একটা অভিনব সত্য প্রচার করিতে পারা সাহসের পরিচয় সন্দেহ নাই; কিন্তু এ সাহসে কাজ হয় না, শুধু অকাজ বাড়ে। যেমন, তাঁহার দেখাদেখি আমার অকাজ বাড়িয়া গিয়াছে এবং যে হতভাগ্যেরা এগুলো পড়িবে, তাহাদের ত কথাই নাই। অবশ্য, পুরুষমানুষের সাহস থাকা ভাল, কিন্তু একটু কম থাকাও আবার ভাল। যা হউক কথাটা এই। ঠাকুরমশাই উড়িষ্যার (কলিঙ্গ) খোন্দ এবং বাইবেলের কানানাইটের মধ্যে গুটি পাঁচ-ছয় মিল দেখিয়াই উভয়কে সহোদর ভাই বলিয়া স্থির করিয়াছেন, কিন্তু গরমিলের ধার দিয়াও যান নাই। অবশ্য গরমিল দেখিতে যাইবার অসুবিধা আছে বটে, এবং এই অসুবিধা ভোগ না করিয়াও যা হউক একটা কিছু লেখা যায় সত্য, কিন্তু তাহাকে সত্য আবিষ্কার বলে না। যাহা বলে তাহা পিক্উইক পেপারের আরম্ভটা। তা ছাড়া, শুধু সাদৃশ্য দেখিয়াই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে কত বিপজ্জনক, তাহার একটা সামান্য দৃষ্টান্ত দিতেছি। এই সেদিন চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা থালায় জল লইয়া হাঁ করিয়া বসিয়াছিল।
গ্রহণ লাগিলে তাহারা দেখিবে। হঠাৎ শাশুড়ী ঠাকরুন বলিলেন, “হাঁ বৌমা, কালীচরণ যে পাঁজি দেখে বলে গেল সাতটার পূর্বেই গেরণ লাগবে, সাতটা ত বেজে গেল, কৈ একবার ভাল করে পাঁজিটা দেখ দেখি গা!” দেখিলাম, পাঁজিতে লেখা আছে, ‘দর্শনাভাব’। বলিলাম, “গেরণ হয়ত লাগবে, কিন্তু দেখা যাবে না।” ঠাকরুন বিশ্বাস করিলেন না, বলিলেন, “সে কি কথা বৌমা? কালী যে বেশ করে দেখে বলে গেল, ‘দশানা ভাব’ দেখা যাবে, আর তুমি বলছ একেবারেই দেখা যাবে না? এ কি হয়? দশানা না হউক আটানা, আটানা না হউক চার আনাও ত দেখতে পাওয়া চাই!” কালীচরণকে ডাকানো হইলে আমি আড়ালে থাকিয়া বলিলাম, “সরকারমশায়, পাঁজিতে দর্শনাভাব লেখা আছে—গেরণ ত দেখতে পাওয়া যাবে না।” কালীচরণ হাসিয়া বলিল, “বৌমা, কর্তা স্বর্গে গেছেন—তিনি বলতেন, গাঁয়ের মধ্যে পাঁজি দেখতে যদি কেউ থাকে ত সে কালী। ঐ যার নাম দর্শনাভাব, তারই নাম দশানাভাব। শুদ্ধ করে লিখতে গেলে ঐ রকম লিখতে হয়। এ বড় শক্ত বিদ্যে বৌমা, পাঁজি দেখে দেওয়া যে-সে লোকের কাজ নয়!” আমি অবাক্ হইয়া গিয়া ‘রেফের’ উল্লেখ করিয়া বলিলাম, “শ’য়ের মাথায় ঐ খোঁচাটার মত তবে কি রয়েচে? ‘আ’-কার এদিকে না থেকে ওদিকে কেন?” কিন্তু আমার কোন কথাই খাটিল না। কালীচরণ সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়াছে—সে হটিল না। বরং আরো হাসিয়া বলিল, “বৌমা, ওগুলো শুধু দেখবার বাহার। ছাপাড়েরা মনে করেছে, ঐগুলো দিলে বেশ দেখতে হবে। শোননি, লোকে কথায় বলে—যেন ছাপাড়ের বিদ্যে! ওগুলো কিছুই নয়।” এই বলিয়া সে ‘দর্শনাভাব’কে’ ‘দশানা ভাবে’ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া জয়োল্লাসে হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল। তবু, সে বাড়ির গোমস্তা—ব্যাকরণ পড়ে নাই। সে-রাত্রে যদি সে ঠাকুরমশায়ের মত ‘র-ল-ড-লয়োরভেদঃ’ শুনাইয়া দিতে পারিত, তাহা হইলে আমার আর মুখ দেখাইবার পথ থাকিত না। যাই হউক, এ-সব ঘরের কথা,—না বলিলেও চলিত এবং কালীচরণ শুনিলে হয়ত দুঃখ করিবে, কিন্তু সামান্য ‘রেফ’টাকে তুচ্ছ করিয়া, ‘দর্শনাভাব’টাও যে দশানাভাবে দাঁড়ায়, এমন কি সাদৃশ্যের জোরে এবং ‘র-ল-ড’য়ের সাহায্যে এশিয়া মাইনরের কানানাইটও যে কলিঙ্গের কানকাটায় ষোল আনা রূপান্তরিত হয়, এই তুচ্ছ কথাটাই আজ ঠাকুরমশায়কে সবিনয় নিবেদন করিবার বাসনা করিয়াছি। এখন কোন পাঠক যদি ধরিয়া বসে, দশানাটা বুঝি, ষোল আনাটা কি? তাহা এই। উক্ত প্রবন্ধে ঠাকুরমশায় শুরুতেই বলিতেছেন—“পাঠক শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, এই কানানাইটদিগের সহিত [উড়িষ্যার] কানকাটার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে’ (দশানাভাব)। পরেই বলিতেছেন—“কানানাইটরা ইস্রেল-প্রবাসী কানকাটা ছাড়া আর কিছুই নয়” (ষোল আনা ভাব)। পাঠকেরা যে রীতিমত বিস্মিত হইবে, তাহা তিনি ঠিক ধরিয়াছেন। এমন কি, চন্দ্রগ্রহণের রাত্রের অপেক্ষাও।
যাহা হোক, এই ষোল আনার স্বপক্ষে ঠাকুরমশায় বলিতেছেন—“ইহাদিগের উভয়ের দেবতা, উভয়ের আচার-প্রথার মধ্যে আশ্চর্য সাদৃশ্য। উভয় জাতির আচার-প্রথা উহাদিগের দেবদেবী ইত্যাদি সকল বিষয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কানানাইট ও কানকাটা উহারা উভয়ে একজাতীয় জীব।…প্রথমে উহাদের দেবতা ও নরবলি-দানপ্রথা বিষয়ে যে কিরূপ ঐক্য, তাহাই দেখাইতেছি। ভারতের কানকাটা বা কন্দকাটারা যদিও নানা দেবদেবীর উপাসনা করে বটে, কিন্তু তাহাদের সর্বপ্রধান দেবতা—ভূমির উর্বরা-শক্তির দেবতা বা ভূ-দেবী ‘তরী বা ‘তাড়ী’। ভূমির উর্বরা-শক্তি এই দেবীর উপরেই নির্ভর করে বলিয়াই তাহাদের বিশ্বাস। এই দেবীর সন্তোষের জন্যই বিশেষ কর্মে তাহারা নরবলি বা শিশুবলি দিতে প্রবৃত্ত হয়।” এই উভয় জাতির দেবতা যে একই দেবতা, তাহা দেখাইবার জন্য ঋতেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, “কানানাইটদিগেরও প্রধান দেবতা—উর্বরা-শক্তির দেবী। Their chief deity Astart, the goddess of fertility”। “কন্দদিগের ভূ-দেবী তরী বা তাড়ী (Tari) ও কানানাইটদিগের দেবী Ishtar (স্টার) বা Astarte (আসটার্ট)—উহারা একই শব্দের বিভিন্ন রূপ মাত্র, কেবল দেশভেদে উচ্চারণভেদ ঘটিয়া সামান্য বৈলক্ষণ্য উৎপাদন করিয়াছে। যেমন, সংস্কৃত ‘তার’ বা ‘তারকা’ শব্দে পূর্বে ‘s’ যুক্ত হইয়া star হইতে দেখা যায়, সেইরূপ এই ‘তারী’ শব্দেরও পূর্বে ‘s’ বা ‘as’ যুক্ত হইয়া Ishtar বা Astarte-রূপে পরিণত হইয়াছে। উচ্চারণকালে ‘ট’য়ে ‘ড়’য়ে বিশেষ প্রভেদ নাই।” ইত্যাদি, ইত্যাদি, যেহেতু ‘র-ল-ড-লয়োরভেদঃ’। প্রথমে এই দেবীটির আলোচনা প্রয়োজন। ঐক্য যাহা থাকিবার, তাহা ত উনিই একরকম দেখাইয়াছেন, অনৈক্য কোথায়, তাহাই বলা আবশ্যক।
ঋতেন্দ্রবাবু যাই দেখিতে পাইলেন ‘উর্বরা-শক্তি’ অমনি দুইটাকে এক করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু উর্বরা-শক্তি মানে কি জমিরই উর্বরা-শক্তি? নারীর সন্তান প্রসব করিবার শক্তিকে কি বলে? উহার কথাটা ঐ পর্যন্ত সত্য যে, উভয় জাতিই উর্বরা-শক্তির পূজা করিত, কিন্তু কানানাইটরা যে উর্বরা-শক্তির পূজা করিত তাহা জমির নয়, নারীর। কারণ, যে চিহ্ন (Symbol) দ্বারা আসটার্ট দেবীটিকে প্রকাশ করা হইত, এবং যে কারণে দেবীর মন্দিরে ‘temple prostitution’ প্রচলিত ছিল, এবং যেহেতু “the licentious worship of the devotees of Astarte in her temple in Tyre and Sidon rendered the names of these cities synonymous with all that was wicked” তাহা ভূমির উর্বরা-শক্তি হইতেই পারে না। পুরাতন ধর্ম-সম্বন্ধীয় ইতিহাসের যে-কোন একটা খুলিয়া দেখিলেই পাওয়া যায়, Astarte কে Venus-দেবীর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। যথা—Astarte, the Syrian Venus। ‘ভীনস্’ ভূ-দেবী নয়। আরো একটা কথা, এই খোন্দদিগের তাড়ী দেবীর মত কানানাইটদের আসটার্ট সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ছিলেন না। ইনি ‘বাল’ দেবতার পত্নীরূপেই পূজা পাইতেন। দেশে যতগুলি ‘বালিম’ ছিলেন ততগুলিই বিভিন্ন আসটার্ট ছিলেন।
এমন কি, এই দেবীটিকে কোন কোন স্থানে ‘শেম্বাল’ পর্যন্ত বলা হইয়াছে। ‘শেম্বাল’ অর্থে বালদেবতার ছায়া। ইনি পরে পরে অনেকগুলি নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। (2. Kings 23. 13)। বাইবেলে আল্টারথ বলা হইয়াছে। আলেন সাহেব একস্থানে বলিয়াছেন, “The Astarte given to Hellas under the alias of Aphrodite came back again as Aphrodite to Astarte’s old Sanctuaries”। কিন্তু ইহার সাবের নাম ছিল ‘আশেরা’ সুতরাং ‘তাড়ী’র সহিত যদি কাহারো সম্বন্ধ থাকা উচিত ত এই আশেরার, আসটার্টের নয়। আমার ব্যাকরণে তেমন বোধশোধ নাই, থাকিলেও যে এই ‘আশেরা’ শব্দটাকে ‘র-ল-ড’ইয়ের জোরে ‘তাড়ী’ করিয়া তুলিতে পারিতাম, সে ভরসা ত জোর করিয়া পাঠককে দিতে পারিলাম না। তারপরে নরবলির কথা। পৃথিবীর যে-সমস্ত প্রাচীন জাতি ভূ-দেবীর পূজা করিত এবং প্রসন্ন করিতে নরবলি দিত, তাহাদের মধ্যে না পাই কোথাও আসটার্ট দেবীকে, না পাই তাঁহার ভক্ত কানানাইটদিগকে। পাইলেও ত মনে হয় না, এমন কিছু প্রমাণ করিত যে, খোন্দ এবং কানানাইট একই ধর্মের আইন-কানুন মানিয়া চলিয়াছিল। দক্ষিণ-আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা (Indians of Guayaquil) জমিতে বীজ বপন করিবার দিনে নরবলি দিত। প্রাচীন মেক্সিকোর অধিবাসীরা “Conceiving the maize as a personal being who went through the whole course of life between seed time and harvest, sacrificed new-born babes when the maize was sown, older children when it has sprouted and so on till it was fully ripe when they sacrificed old men.” পাউনিরা ভূমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধি করিতে প্রতি বৎসর নরবলি দিত। দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রাচীন কঙ্গোর রানী “used to sacrifice a man and woman in March; they were killed with spades and hoes.” গিনি প্রদেশের অনেক স্থানেই “It was the custom annually to impale a young girl alive soon after the spring equinox in order to secure good crops. A similar sacrifice is still annually offered at Benin.” বেচুয়ানা জাতিরাও ভাল ফসল পাইবার জন্য নরবলি দিত। আমাদের ভারতবর্ষের গোঁড়েরাও এক সময়ে ভূমির উর্বরা-শক্তি বৃদ্ধি করিতে ব্রাহ্মণশিশু চুরি করিয়া আনিয়া ভূ-দেবীর সম্মুখে বিষাক্ত তীর দিয়া বিদ্ধ করিয়া হত্যা করিত। অস্ট্রেলিয়ার অসভ্য অধিবাসীরাও একটি কন্যাকে জীবন্ত পুঁতিয়া ফেলিয়া ভূ-দেবীকে প্রসন্ন করিত এবং সেই গোরের উপর সমস্ত গ্রামের শস্যবীজ চুপড়িতে করিয়া রাখিয়া যাইত।
তাহারা বিশ্বাস করিত, মেয়েটি দেব্তা হইয়া ঐ সমস্ত বীজের মধ্যে প্রবেশ করিবে এবং শস্য ভাল হইবে। প্রাচীন মিশরেও “sacrificed red-haired men to satisfy corn-god.” সাইবেরিয়াতেও এই রকম বলির প্রথা ছিল। ইহারা কেহ আমেরিকার, কেহ আফ্রিকার, কেহ এশিয়ার, কেহ অস্ট্রেলিয়ার বাসিন্দা।
একই রকমের ভূ-দেবী পূজা। ঐক্য দেখিয়া মনে হয়, ইহারা সকলেই এক-একবার কানকাটার দেশে আসিয়া শিখিয়া গিয়াছিল। কিন্তু, কবে কেমন করিয়া আসিয়াছিল, সে কথা ইতিহাসে লেখে না, অতএব বলিতে পারিলাম না। ঠাকুরমশায় Encyclopaedia Britannica হইতে উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন “কানানাইটের দেশে numerous jars with the skeletons of infants পাওয়া গিয়াছে, এবং we cannot doubt that the sacrificing of children was practised on a large scale among the Cananites.” এ ঠিক কথা। কানানাইটরা শিশু বলি দিয়া কটাহের মধ্যে আশেরা দেবীকে নিবেদন করিত; কিন্তু তিনি কোথায় পাইলেন—খোন্দেরাও শিশু বলি দিয়া ভূ-দেবীকে নিবেদন করিত? তাহারাও শিশুহত্যা করিত সত্য, কিন্তু সে হত্যা দেবতার নৈবেদ্যের জন্য নয়। অনেকটা দারিদ্র্যের ভয়ে, অনেকটা ভূত-প্রেতের দৃষ্টি লাগিয়াছে এই কুসংস্কারে। হত্যা করা মানেই বলি দেওয়া নয়। তবে, কানানাইটের কটাহের (jars) সঙ্গে এইটুকু মাত্র ঐক্য আছে যে, কন্দকাটারাও বড় বড় জালা জলপূর্ণ করিয়া তাহাতে শিশুটিকে ডুবাইয়া মারিত। কারণ, আর কোনরূপে হত্যা করা তাহারা বিধিসঙ্গত মনে করিত না। কথাটা কোথায় পড়িয়াছি, মনে করিতে পারিতেছি না, কিন্তু কোথায় যেন পড়িয়াছি, কে একজন এক বৃদ্ধ খোন্দকে প্রশ্ন করিয়াছিল, “বাপু, তোমরা এমন যন্ত্রণা দিয়া শিশুবধ কর কেন, আর কোন সহজ উপায় অবলম্বন কর না কেন?” সে জবাব দিয়াছিল, “এ ছাড়া আর কোন উপায়ে মারা ভয়ঙ্কর ‘পাপম্’। কটাহের ঐক্য এই যা। সে দশ আনাই হউক আর ষোল আনাই হউক।
ঋতেন্দ্রবাবু বাইবেলের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, “শিশুঘাতক কানানাইটরা যে সকলকে কিরূপ বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল” ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কলিঙ্গের খোন্দেরা কবে কাহাকে এমন করিয়া বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিল, এবং কোন্ দিন কাহার ছেলেমেয়ে চুরি করিয়া আনিয়া দেবতার পূজা দিয়াছিল, তাহা আমার জানা নাই। তাহারা যাহাকে ভূ-দেবীর নিকটে বলি দিত, তাহাকে ‘মিরিয়া’ বলিত, এবং এই ‘মিরিয়া’, তা সে নর-নারী যেই হউক, যৌবনপ্রাপ্ত না হইলে কিছুতেই দেবতাকে উৎসর্গ করা হইত না। তাহারা কানানাইটদের মত ছেলে চুরি করিয়া আনিয়া যে বলি দিত না, তাহার একটা বড় প্রমাণ এই যে, তাহারা মরণাপন্ন ‘মিরিয়া’র কর্ণমূলে এই কথা উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিতে থাকিত, “তোমাকে দাম দিয়া কিনিয়াছি—আমাদের কোন পাপ নাই—কোন পাপ নাই—আমরা নির্দোষ।” কিন্তু কানানাইটদের সম্বন্ধে এরূপ কিছু আবৃত্তি করিবার নিয়ম ছিল কি? ছিল না। ঋতেন্দ্রবাবু নিজেও প্রবন্ধের এক স্থলে ম্যাকফার্সন সাহেবের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, খোন্দেরা আর যাহাই হউক, চোর-ডাকাত ছিল না। তা ছাড়া, কানানাইটদের দেবমন্দিরে শিশুর পঞ্জর দেখিতে পাওয়াটা ঠাকুরমশায়ের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেয় না, বরং বিপক্ষে দেয়।
তিনি লিখিয়াছেন, “কানানাইটদের দেবমন্দিরাদি খনন করিতে করিতে পুরাতত্বানুসন্ধানীরা এমন সব বৃহদাকার পাত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহার মধ্য হইতে শিশুর সমগ্র পঞ্জর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এ-সকলই দেবোদ্দেশে শিশু-বলিদানের নিদর্শন বলিয়া পণ্ডিতেরা স্বীকার করেন।”
আমিও করি। কিন্তু, তিনি একটু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেই দেখিতে পাইতেন, ইহাদের বলির শিশুগুলি ভূমির উর্বরা-শক্তি বৃদ্ধিকল্পে ভূ-দেবীকে উৎসর্গ করা হইলে তাহাদের সমগ্র অস্থিপঞ্জর পাওয়া ত ঢের দূরের কথা, এক টুকরা হাড়ও মিলিত না। কারণ, পূর্বেই দেখিয়াছি, যাহারাই ভূ-দেবীর প্রীত্যর্থে নরবলি দিয়াছে, তাহারাই মৃতদেহটাকে কোন-না-কোন রকমে ভূমির সঙ্গেই মিশাইয়া দিয়াছে। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানীর জন্য কটাহে করিয়া তুলিয়া রাখিয়া যায় নাই। উড়িষ্যার কন্দকাটারাও রাখে নাই। তাহারা মৃতদেহটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া গ্রামের সকলে মিলিয়া ভাগ করিয়া লইয়া যে যাহার নিজের ক্ষেতে পুঁতিত। এমন কি, অবশিষ্ট নাড়িভুঁড়ি হাড়গোড়গুলোকেও ছাড়িত না। দগ্ধ করিয়া জলে গুলিয়া জমিতে ছিটাইয়া তাহার উর্বরা-শক্তি বৃদ্ধি করিয়া তবে ক্ষান্ত হইত। এত দূর ত দেবীমাহাত্ম্যে এবং তাঁহার পূজার নৈবদ্যে কাটিল। ইহাতে ঐক্য এবং অনৈক্য যাহা আছে, তাহা বিচার করিবার ভার পাঠকের উপরে।
ঋতেন্দ্রবাবু এইবার দ্বিতীয় ঐক্যের অবতারণা করিয়াছেন। বলিতেছেন, “যে যেখানে থাকে, তাহার সেই আবাসস্থানের তুল্য প্রিয় আর কি হইতে পারে? তালগাছ কানাকাটাদের আবাসবৃক্ষ; এই কারণে তালগাছ ত উহাদের প্রিয় হইবেই। আবার এই তালগাছপ্রিয়তা কানানাইটের মধ্যেও বড় অল্প লক্ষিত হয় না। কানানাইটরাও বড় তালগাছভক্ত জাতি। তালজাতীয় বৃক্ষ উহাদের এতই প্রিয় যে, কানানাইটদের অন্যতম শাখার নাম ফিনীসিয়। (শব্দের উৎপত্তি তালজাতীয় গাছের নাম হইতে আসিয়াছে। ফিনীসিয় শব্দের উৎপত্তি ‘ফইনিক’ শব্দ হইতে, উহার অর্থ ‘তালের দেশ’—Phoenike signify the land of palms)”—যদিও ‘ফইনস’ অর্থাৎ লাল রং (scarlet) হইতেও ফিনীসিয়া হওয়া অসম্ভব নয়। যা হউক, ঋতেন্দ্রবাবুর এ যুক্তিটা ঠিক বোঝা গেল না। কারণ, দেশের ভাল গাছটিকে ভালবাসার মধ্যে লওয়াতে আশ্চর্য হইবার বিষয় ত কিছুই দেখিতে পাই না। কন্দকাটাদের দেশে বিস্তর তালগাছ। তাহারা তালের কড়ি বরগা করে, পাতায় ঘর ছায়, চাটাই বুনিয়া শয্যা রচনা করে। বাইবেলের কানানাইটরাও পাম (palm) বড় ভালবাসে। কারণ, ‘পাম’ তাহাদের দেশের একটি অতি উপকারী বৃক্ষ এবং দেশে আছেও বিস্তর। কিন্তু ইহাতে কি প্রমাণ করে? আমাদের হুগলি জেলার আমগাছ, তা ফলও ভাল, কাঠও ভাল, আছেও অনেক। আমরা আমগাছ ভালবাসি। বর্ধমান জেলায় কাঁঠালগাছ বিস্তর। তারা ওটা খায়ও বেশি, গাছটাকেও স্নেহ করে—ইহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে? কিন্তু ঋতেন্দ্রবাবু বলিতেছেন, “কারণ কি?
উভয়েরই জাতিগত একতা ও উভয়ের এক আদিম বাসভূমিই উহার কারণ।” কিন্তু কেন? দেশের উপকারী গাছকে ভালবাসাই ত সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। বরং উনি যদি দেখাইতে পারিতেন, কোন একটা বৃক্ষকে ভালবাসিবার ঠিক হেতু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, অথচ, উভয় জাতিই ভালবাসিয়াছে, তাহা হইলে একটা কথা হইতে পারিত। যেমন, শেওড়া গাছ। যদি দেখান যাইত, ঠাকুরবাড়ির (জগন্নাথ) লোকেও গাছটাকে শ্রদ্ধা করে এবং উড়িষ্যার কানকাটারাও করে, অথচ, কেন করে বলা যায় না, তাহা হইলে নিশ্চয়ই উহাদের একজাতীয়তা সন্দেহ হইতে পারিত, কিন্তু এ স্থলে কৈ, কিছুই ত চোখে ঠেকে না। আরো একটা কথা। কলিঙ্গ দেশের কানকাটার ‘পাম’ তালগাছ, কিন্তু বাইবেলের কানানাইটদের দেশের ‘পাম’ খেজুরগাছ। দুটোকেই সাহেবেরা ‘পাম’ বলে, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা কি এক? ফলের চেহারাতেও একটু প্রভেদ আছে, ওজনেও একটু কম-বেশি আছে। তাল ফলটা খেজুর ফলটার চেয়ে একটু বড়। একসঙ্গে রাখিলে মিশিয়া যায় না, তাহা বোধ করি ঋতেন্দ্রবাবুও অস্বীকার করিবেন না। ভোজন করিতেও একরকম মনে হয় না। অতএব গাছ দুটোকে সাহেবরা যা ইচ্ছা বলুক, এক নয়। একটা তাল একটা খেজুর।
ঋতেন্দ্রবাবুর চতুর্থ ঐক্য। বলিতেছেন, “এইবারে পাঠকগণ আর একটি বিষয়ে কলিঙ্গ বাসী কানকাটা ও কানানাইটদিগের মধ্যে একতা লক্ষ্য করুন। সেটি উহাদের উভয়ের জাতিগত রক্তবর্ণপ্রিয়তা।…তাহারা কি পুরুষ, কি রমণী, সকলেই ঘোর লাল রঙের কাপড় পরিতে পারিলে অন্য কাপড় চায় না। বিশেষতঃ গঞ্জাম, বিশাখাপত্তন প্রভৃতি তাল কলিঙ্গ বা কানকাটার দেশের লোকেরা কাপড়ের পাকা লাল বেগুনি রঙ করিতে সিদ্ধহস্ত। কানকাটারাও ঠিক কলিঙ্গবাসীদের ন্যায় বড় লাল রঙের প্রিয়। কানানাইটদের অন্যতম শাখা ফিনীসিয়েরা কাপড়ের ঘোর লাল রঙ করিবার জন্য এতটা প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে, অনেকে অনুমান করেন যে, ‘ফইনস’ শব্দ হইতে তাহাদের ফিনীসিয়া নামের উৎপত্তি হইয়াছে।” ঘোরতর একতা আছে, তাহা অস্বীকার করিতে পারিলাম না। কিন্তু দুই-একটা নিবেদনও আছে। প্রথম, এই যে ফিনীসিয়রা যে লাল রঙের কাপড় তৈরি করিত, তাহা ঘরে পুরিয়া রাখিত না, দেশে-বিদেশে বিক্রয় করিত। যাহারা দাম দিয়া কিনিত, তাহারাও লাল রঙটা পছন্দ করিত, এ অনুমান বোধ করি খুব অসঙ্গত নয়। বস্তুতঃ তখনকার লোকেরা লাল রঙটার এত অধিক আদর করিত যে ফিনীসিয়দের ঐশ্বর্য মুখ্যতঃ লাল রঙের কারবারেই। তাহারা, যে সমস্ত জাতি বলিদান দিয়া ঠাকুর পূজা করিত, ঠাকুরকে রক্তপান করাইত, তাহার সকলেই লাল রঙ ব্যবহার করিতে ভালবাসিত। কেন বাসিত, কেন দেব-দেবীকে লাল রঙের কাপড় পরাইত, কেন লাল ফুল, লাল জবা, লাল চন্দন দিয়া সন্তোষ করিতে চাহিত, সে আলোচনা করিতে গেলে অনেক কথা বলিতে হয়। এ প্রবন্ধে তাহার স্থান নাই, আবশ্যকও নাই।
সুদ্ধ এই স্থূল কথাটা বলিয়াই ক্ষান্ত হইতে চাই যে, কেবল এই দুটো জাতিই ঘোর লাল রঙ ভালবাসিত না, সে সময়ে জগতের বার আনা লোকেই ভালবাসিত। তার পরে রঙ তৈরির কথা। বিদ্যাটা খুব সম্ভব ফিনীসিয়েরাও কানকাটার কাছে শিখে নাই, কানকাটারাও ফিনীসিয়ের কাছে শিখে নাই। কানকাটারা অর্থাৎ কলিঙ্গ বাসী খোন্দেরা, গাছের রস এবং তৃণমূল দিয়া রঙ তৈরি করিত, কিন্তু ফিনীসিয়েরা মুরে মাছের (Murex-purple shell-fish) মাংস সিদ্ধ করিয়া রঙ করিত। সুতরাং, বিদ্যাটা একত্র অর্জন করা হইয়া থাকিলে একরকম হওয়াই সম্ভব ছিল। ও মাছটা কানকাটার দেশের সমুদ্রেও দুষ্প্রাপ্য নয়। আর লাল রঙ ভালবাসাবাসিটা কি একটা তুলনার বস্তু হইতে পারে? উভয়ে জাতির চেহারায় সাদৃশ্য ছিল কি না, এ-সব কোন কথাই উঠিল না। কথা উঠিল উভয়েই লাল রঙ ভালবাসিত। এ-রকম ঐক্য আরো আছে। উভয় জাতিই চোখ বুজিয়া ঘুমাইতে ভালবাসিত, হাতে কিছু না থাকিলে হাত দুলাইয়া চলিতে পছন্দ করিত,—এ-সব ঐক্যের অবতারণাই বা না করিলেন কেন?
ঠাকুরমশায়ের পঞ্চম ঐক্য—নামে। এটি সবচেয়ে চমৎকার। বলিতেছেন, “কানানাইট-বংশীয় যে লোকটা ইস্রেলরাজ ডেভিডের শরীররক্ষী ছিল, তাহার নাম ছিল উড়িয়া (Uriha) এবং এই উড়িয়া নামটি কাকতালীয়বৎ হয় নাই। কেননা, কানানাইটেরা যে কলিঙ্গ বা উড্র-দেশীয় লোক, সেকালে সকলেরই জানা ছিল। সেই কারণেই যেমন নেপালী বা ভুটিয়া ভৃত্য থাকিলে তাহার নিজ নামের পরিবর্তে নেপালী বা ভুটিয়া নামেই পরিচিত হয়, এ-ক্ষেত্রেও সেইরূপ হইয়াছে। উড্র হইতে উড়িয়ার উৎপত্তি। ইস্রেলী ভাষায় কি দেশের নামে, কি নামে, ‘ইয়া’-অন্ত শব্দের প্রচলন বড় অধিক। যথা—জোসিয়া, জেডেকিয়া, হেজেকিয়া, সিরিয়া ইত্যাদি।” এই কারণেই ‘উড্র’ শব্দের উপর ‘ইয়া’-অন্ত শব্দ লাগাইয়া ইস্রেলী ভাষায় উড়িয়া হইয়াছে। আমারও ছেলেবেলায় ডেভিড কপারফিল্ডের উড়িয়া হিপকে উড়ে মনে হইত। ভাবিতাম, লোকটা বিলেত গেল কিরূপে? এখন দেখিতেছি কিরূপে গিয়াছিল! আরও ভাবিতেছি, স্কানডেনেভিয়া, বটেভিয়া, সাইবিরিয়া প্রভৃতিও সম্ভবতঃ এমনি করিয়াই হইয়াছে। কারণ, এগুলোও একটা শব্দ কিনা দারুণ সন্দেহ। বরং ইস্রেলী ‘ইয়া’ প্রত্যয়ে নিষ্পন্ন হওয়াই সঙ্গত এবং স্বাভাবিক। অতএব, ‘উড়িয়া’ যে একটা শব্দ নয়, ইহা “উড্র+ইয়া” তাহাও যেমন নিঃসংশয়ে অবধারিত হইল, সেকালে সকলেই যে জানিত কানানাইটরা উড্রদেশীয়, তাহাও তেমনি অবিসংবাদে স্থিরীকৃত হইল। বেশ! তবে, একটা তুচ্ছ কথা এই যে, উড়িয়া লোকটা ছাড়া আরও বিস্তর ‘উড়িয়া’ কানানাইট তথায় ছিল। ইস্রেলদের সঙ্গে অনেক দিন অনেক রকমেই তাহাদের আলাপ।
লড়ায়েও বটে, বিয়াসাদিতেও বটে। আনন্দেও বটে, নিরানন্দেও বটে। বাইবেল গ্রন্থে নাম করা হইয়াছেও অনেকবার, কিন্তু এমনি আশ্চর্য যে, তাহাদের কোন স্বদেশীয়কেই আর ‘উড়িয়া’ বলিয়া আদর করিতে শুনিলাম না। বোধ করি ইস্রেলরাজ ডেভিডের নিষেধ ছিল। বলা যায় না—হইতেও পারে। ষষ্ঠ ঐক্যের অবতারণা করিয়া ঠাকুরমশায় বলিতেছেন, “রাজা ডেভিড যে উড্র-সন্তান কানানাইটাকে তাঁহার শরীররক্ষক প্রহরীর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবতঃ তাহাদের জাতিগত গুণ দেখিয়া। বর্তমান কালে সে কানানাইট জাতির অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই একই গোষ্ঠীর কন্দকাটা এখনও ভারতের কলিঙ্গ বা উড্রদেশে বিদ্যমান। এই কন্দকাটার শারীরিক সুদৃঢ় গঠন দেখিলেই বুঝা যায় যে, বাস্তবিক তাহার শরীররক্ষক-পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য! সুদ্ধ ইহাই নহে, রাজপ্রহরীর যে-সকল গুণ থাকা আবশ্যক, সে-সকলও তাহাদের জাতির সাধারণ ধর্ম বলিয়া গণ্য। কাপ্তেন ম্যাকফার্সন লিখিয়াছেন’,—’মিথ্যা কথা, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, গোপনীয় কথার প্রকাশ, এ-সকল কন্দেরা অধর্ম এবং বীরত্বের ন্যায় যুদ্ধে প্রাণত্যাগ ও যুদ্ধে শত্রুনাশ ধর্ম বলিয়া গণ্য করে’।” বেশ কথা। এই জন্য আমিও ইতিপূর্বে বলিয়াছি, খোন্দেরা কানানাইটদের মত পরের ছেলে চুরি করিয়া বলি দিত না। কিন্তু খোন্দেরাই কি কানানাইটদের গোষ্ঠী, ফিনীসিয়রা নয়? ঋতেন্দ্রবাবুও ইতিপূর্বে দেখাইয়াছেন, এবং আমিও তাহার প্রতিবাদ করি নাই যে, কানানাইটরা ফিনীসিয়দের উপশাখা মাত্র। এবং এইজন্যই তিনি লাল রঙ – প্রিয়তা, লাল রঙ তৈরির ক্ষমতা, তালগাছ বা খেজুরগাছে স্নেহ, ‘ফাইনস’ শব্দ ইত্যাদি প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া ফিনীসিয়দের সহিত অভিন্নতা প্রমাণ করিতে যত্ন করিয়াছেন। বস্তুতঃ ফিনীসিয় ও কানানাইটে প্রভেদ নাই। প্রবন্ধের শেষে তিনি নিজেও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, “ফিনীসিয়রা কানানাইট জাতির অন্যতম শাখা।” কিন্তু এই ফিনীসিয়দের নৈতিক চরিত্রটা কিরূপ? ইস্কুলের ছেলেরাও জানে, ফিনীসিয়রা চুরি–ডাকাতি, বিশ্বাসঘাতকতা, নরহত্যা প্রভৃতি সর্বপ্রকার পাপেই সিদ্ধহস্ত ছিল। বাণিজ্য করিতে বিদেশে গিয়া নিজেদের নৌকা বা জাহাজ কোথাও লুকাইয়া রাখিয়া মাল–মসলা বিদেশী ক্রেতাদের সম্মুখে খুলিয়া ধরিত এবং যখন তাহারা নিঃসন্দিগ্ধ –চিত্তে কেনা–বেচায় মগ্ন থাকিত, সুবিধা বুঝিয়া এই ফিনীসির ডাকাত বণিক তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া লুটপাট করিয়া লইত এবং যাহাকে পারিত ধরিয়া লইয়া নিজেদের জাহাজে উঠিয়া পাল তুলিয়া দিত।
ইহাদিগকেই অন্যত্র দাসরূপে বিক্রয় করিয়া অর্থ অর্জন করিত। বাস্তবিক, এমন অন্যায়, এমন অধর্ম, এমন নিষ্ঠুরতা ছিল না, যাহা এই ফিনীসিয়রা না করিত। দিনে যাহারা অতিথি হইত, রাত্রে তাহাদের গলাতেই ছুরি দিত। এ-সব ইতিহাসের প্রমাণ-করা কথা। অনুমান বা কল্পনা নহে। এমন জাতির জ্ঞাতি হইয়াও উড়িষ্যার কন্দকাটারা এত বড় ধার্মিক হইল কিরূপে? এবং এই ফিনীসিয় শরীররক্ষী উড়িয়াই বা এমন যুধিষ্ঠির হইলেন কি মনে করিয়া? ঋতেন্দ্রবাবু যদি এতটুকু বৈজ্ঞানিক বিচারপদ্ধতি অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে দেখিতে পাইতেন, ফিনীসিয়রা বা কানানাইটরা উড়িষ্যার খোন্দ জাতি হইলে নৈতিক চরিত্রে এমন আকাশ-পাতাল ব্যবধান হইত না। ইহার পরে তিনি রথের প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিয়াছেন, “ইস্রেলরাজ [সলোমন] যে-সকল বিষয়ে কলিঙ্গবাসীদের অনুসরণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রথ ও মন্দিরাদি নির্মাণই প্রধান উল্লেখযোগ্য।… কলিঙ্গবাসীরা চিরদিন রথের আড়ম্বরে আকৃষ্ট, রথের ধুমধাম, রথের জাঁকজমক কলিঙ্গের চারিদিকে।…সলোমনের এক সহস্র চারি শত রথ নির্মিত হইয়াছিল।” হয় নাই এ কথা কেহ বলে না। রাজা সলোমন অনেকগুলি লড়াই করিবার রথ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ঋতেন্দ্রবাবু বলিয়াছেন, কলিঙ্গসন্তানেরা সেগুলি গড়িয়া দিয়াছিল। তাহা হইতে পারে এবং না হইতেও পারে। হইতে পারে এইজন্য যে, ঠাকুরমহাশয়ের নিশ্চিত বিশ্বাস হইয়াছে যে, ফিনীসিয়রা উড়ে-দেশের লোক। উড়ে-দেশের জগন্নাথের রথ আছে, সুতরাং তাহারাই সলোমনের রথ তৈরি করিয়াছিল। আমার বিশ্বাস হয় না যে এইজন্য যে, একে ত ফিনীসিয়রা উড়ে নয়, তা ছাড়া রথ গড়িবার লোক আরও আছে। সলোমনের সময়ে, অর্থাৎ যীশুখ্রিস্টের হাজার বৎসর পূর্বে কলিঙ্গে রথের ধুমধাম কিরূপ ছিল এবং তাহারা কিরূপ রথ তৈরি করিতে পারিত, আমার তাহা জানা নাই। দ্বিতীয় কারণ, রাজা সলোমনের প্রতিবাসী মিশরীয়েরা বহু পূর্ব হইতে সুন্দর এবং মজবুত রথ করিবার জন্য বিখ্যাত ছিল। তাহাদিগের রথাদি কিরূপে তৈরি হইত, তাহা দ্বিবিধ কি ত্রিবিধ, কি কাঠের চাকা তৈরি হইত, সারথিরা কি কি জায়গীর প্রাপ্ত হইত, রথ চালানো তাহাদিগকে জিমন্যাস্টিকের মত কিরূপে রীতিমত অভ্যাস করিতে হইত, ইত্যাদি অনেক কথা বাল্যকালে মিশরের ইতিহাসে পড়িয়াছি। তাহা মনে নাই। মনে রাখিবার আবশ্যকও তখন দেখি নাই। কিন্তু এটা মনে আছে যে, প্রাচীন মিশরীয়েরা চমৎকার রথ গড়িতে পারিত। এবং ইহাও মনে হইতেছে, কিছুদিন পূর্বে Struggle of the Nations পুস্তকের দ্বিতীয় কি তৃতীয় অধ্যায়ে দেখিয়াছি, একজন আসীরিয় রাজা ফারাওর (মিশরের রাজা) নিকট পরাজিত হইয়া এই বলিয়া দুঃখ করিয়াছিল, “যদি উহাদের মত লড়াই করিবার রথ থাকিত, তাহা হইলে এ দুর্দশা ঘটিত না।”
ফল কথা, তখনকার লোক রথের উপকারিতা বুঝিত এবং সলোমনের মত বুদ্ধিমান ও ভুবনবিখ্যাত নরপতিও তাহা বুঝিয়াছিলেন এবং সেইজন্যেই অত রথ তৈরি করাইয়াছিলেন। কিন্তু কথা এই, কে গড়িয়াছিল? উড়িষ্যাবাসীরা কিংবা মিশরবাসীরা?
বাইবেল গ্রন্থে লেখা আছে, রাজা সলোমন মিশরের রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং মিশরের সহিত আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। “(1. Kings-3.1. and Solomon made affinity with Pharaoh, king of Egypt and took Pharaoh’s daughter &c)”। এমন অবস্থায় কেমন করিয়া নিঃসংশয়ে স্থির করা যাইতে পারে, রথগুলি কুটুম্ব এবং প্রতিবাসী মিশরীয়েরা গড়িয়া দেয় নাই, দিয়াছিল কলিঙ্গবাসীর জ্ঞাতি কানানাইটরা। অতঃপর ঋতেন্দ্রবাবু প্রমাণ দিতেছেন, “রাজা সলোমন-প্রতিষ্ঠিত নগরের নাম ‘তাড়মর’—এটি সংস্কৃতমূলক কলিঙ্গ নাম। অর্থাৎ ‘তাল’ বা ‘তাড়’ একই কথা।’ তা হইতে পারে। কেননা, র-ল-ডয়ের জোরে ইতিপূর্বে ‘আশেরা’ ‘তাড়ী’, হইয়াছে। এখন ‘তাল’কে ‘তাড়’ করিতে আপত্তি করিলে লোকে আমাকেই নিন্দা করিবে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ঐ শব্দটা কি কলিঙ্গ ছাড়া আর কোন উপায়েই ইস্রেলী ভাষায় ঢুকিতে পারে না? তা ছাড়া, ‘তাল’টা না হয় ‘তাড়’ হইল, কিন্তু ‘মর’টা কি? যাই হউক, ‘তাড়মর’ সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা নাই, সুতরাং এ বিচার ভাষাবিদেরা করিবেন—আমি চুপ করিয়া রহিলাম। কিন্তু, পরিশেষে আমার একটু বক্তব্যও আছে। সেটা এই যে, “কানকাটা বলে, আমি তালগাছে থাকি, যে ছেলেটা কাঁদে তার কাঁধটি ধরে নাচি” ছড়া—কবির এই গানটির উপর নির্ভর করিয়া ঋতেন্দ্রবাবু টানিয়া বুনিয়া যে-সব ঐক্য সংগ্রহ করিয়া বাইবেলের কানানাইটকে উড়িষ্যার কানকাটা বানাইয়াছেন, তাহার অনৈক্যও আছে। সেইগুলিকে অস্বীকার করা উচিত হয় নাই। হইতে পারে তাঁহার কথাই ঠিক, আমার ভুল, কিন্তু মিল-অমিল যখন দু-ই আছে, তখন উভয়কেই চোখের সুমুখে রাখিয়াই তাঁহার বৈজ্ঞানিক সত্যে উপনীত হওয়া উচিত ছিল। আমি এতক্ষণ এই কথাটাই বলিবার প্রয়াস পাইয়াছি মাত্র, আর কিছুই নয়। তবে বাংলা ভাষায় আমার কিছুমাত্র দখল নাই, তাই হয়ত কথাগুলাও গুছাইয়া বলিতে পারি নাই এবং ঠাকুরমহাশয়ের কাছে তেমন শ্রুতিমধুর ও সুখপাঠ্য করিয়াও তুলিতে পারি নাই। তথাপি আশা করিতেছি, এই অকিঞ্চিৎকর প্রতিবাদ যদি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ত, তিনি নিজগুণে এ ত্রুটি মার্জনা করিয়া লইয়া পড়িবেন, এবং ভবিষ্যতে আর কখন এমন ত্রুটি না করিতে হয়, সে ব্যবস্থাও দয়া করিয়া করিবেন।
ক্ষুদ্রের গৌরব
সে রাত্রে চাঁদের বড় বাহার ছিল। শুভ্র, স্নিগ্ধ, শান্ত কৌমুদী স্তরে স্তরে দিগ্দিগন্তে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। আকাশ বড় নির্মল, বড় নীল, বড় শোভাময়। শুধু সুদূর প্রান্তস্থিত দুই-একটা খণ্ড শুভ্র মেঘ মধ্যে মধ্যে দেখা যাইতেছে। সেগুলা বড় লঘু-হৃদয়।কাছে আসিয়া, আসেপাশে ছুটিয়া বেড়াইয়া চাঁদকে চঞ্চল করিয়া দেয়। আজ তাহা পারে নাই, তাই চন্দ্রমা কিছু গম্ভীর-প্রকৃতি। সে স্থির গাম্ভীর্যের যে কি সৌন্দর্য তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারিব না।
আকাশে স্থান গ্রহণ করিলেই তাঁহার এ শোভা হয় না। তবে মনে হয় যেদিন কবি তাঁহার রূপ দেখিয়া প্রথম আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল, আজ বুঝি তাঁহার সেই রূপ! যে রূপ দেখিয়া বিরহী তাঁহার পানে চাহিয়া প্রিয়তমের জন্য প্রথম অশ্রুমোচন করিয়াছিলেন, আজ বুঝি তিনি সেই রূপে গগনপটে উদিত হইয়াছিলেন; আর যে রূপের মোহে ভ্রান্ত চকোরী সুধার আশায় প্রথম পথে ছুটিয়া গিয়াছিলআজ বুঝি তিনি সেই সুধাকার! নির্নিমেষ-নয়নে চাহিয়া চাহিয়া সত্যই মনে হয়, কি শান্ত, কি স্নিগ্ধ, কি শুভ্র! শুভ্র জ্যোৎস্না উন্মুক্ত বাতায়নপথে সদানন্দের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়াছে। গৃহে দীপ নাই। শুধু সদানন্দ নীচে বসিয়া গাঁজার কলিকায় দম দিতেছে, রোহিণীকুমার মুখপানে চাহিয়া আছে। আর অদূরে কে একজন গাহিয়া চলিতেছে, “যমুনা-পুলিনে কাঁদে রাধা বিনোদিনী”। সদানন্দ ধীরে ধীরে গাঁজার কলিকা নামাইয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল, “আহা”!
তাহার পর চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। আর একবার সে মাথা নাড়িয়া, মনে মনে সেই অসম্পূর্ণ পদটি আবৃত্তি করিয়া লইল—“কাঁদে রাধা বিনোদিনী”।
কবে কোন্ স্নেহরাজ্যে বিরহ-ব্যথায় রাধা বিনোদিনী যমুনা-পুলিনে বসিয়া প্রিয়তমের জন্য অশ্রুমোচন করিয়াছিলেন সে-কথা ভাবিয়া আজ সদানন্দের চক্ষে জল আসিয়াছে। সে গাঁজা খাইতেছেকাঁদিতে বসে নাই। শুধু একটা গ্রাম্য, অতি ক্ষুদ্র, অসম্পূর্ণ পদ অসময়ে তাহার চক্ষে জল টানিয়া আনিয়াছে।
সদানন্দের মুখে ঈষৎ চাঁদের আলো পড়িয়াছিল। সে আলোকে রোহিণীকুমার সদানন্দের চক্ষের জল দেখিতে পাইল। একটু সরিয়া বসিয়া বলিল, “সদা তোর নেশা হয়েছে, কাঁদছিস কেন?”
সদানন্দ গাঁজার কলিকা জানালা দিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। এবার রোহিণী বিরক্ত হইল। দাঁড়াইয়া উঠিয়া কহিল, “ঐ ত তোর দোষ—মাঝে মাঝে বেঠিক হয়ে পড়িস”সদানন্দ কথা কহিল না দেখিয়া বিরক্ত অন্তঃকরণে রোহিণী নিজেই কলিকার অন্বেষণে বাহিরে আসিল।
আর একবার জানালা দিয়া দেখিলসদানন্দ পূর্বের মত মুখ নিচু করিয়া বসিয়া আছে। তাহার এ ভাব রোহিণীর নিকট নূতন নহেসে বিলক্ষণ বুঝিয়াছিল আজ অন্য আশা নাই। তাই গম্ভীরভাবে কহিল “সদাশুগে যাকাল সকালে আবার আসব।”
রোহিণী একটু বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছিলকিন্তু পথে আসিয়াই তাহার মনে পড়িল—সেই কোমল করুণ “আহা”তখন সে হাততালি দিয়া গান ধরিল“যমুনাপুলিনে বসে কাঁদে রাধা বিনোদিনীবিনে সেইবিনে সেই—”
কিছুক্ষণ বিরামের পর আবার সেই গান সদানন্দের কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র সে যুক্তকরে ঊর্ধ্বনেত্রে কাঁদিয়া কহিল— “দয়াময় তুমি ফিরিয়া এস।”
রাধার দুঃখ সে হৃদয়ে অনুভব করিয়াছে, তাই কাঁদিয়াছে; ক্ষুদ্র কবিতার ক্ষুদ্র একটি চরণ তাহার সমস্ত হৃদয় মন্থন করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছে। সেই নির্মল নীল যমুনা; সেই পিককুহরিত জ্যোংস্নাপ্লাবিত সখী-পরিবৃত কুঞ্জবন, সেই বকুল, তমাল, কদম্বমূল; সেই মৃতসঞ্জীবনী বংশী-স্বর; মান অভিমান মিলন, তাহার পর শতবর্ষব্যাপী সেই সর্বগ্রাসী বিরহ! আর ছায়ার মত সেই ভ্রাতৃপ্রেম মাতৃপ্রেম—দয়া, ধর্ম, পুণ্য—এবং তাহার সর্বনিয়ন্তা পূর্ণব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ!
এত কথা, এই দীপ্ত অথচ স্নিগ্ধভাব, এত মাধুরী প্রণোদিত করিবার গৌরব কি এই অসম্পূর্ণ নিতান্ত সাধারণ পদটির? রচয়িতার, না গায়কের? কিন্তু পদটি যদি “যমুনা-পুলিনে বসে কাঁদে রাধা বিনোদিনী” না হইয়া “কাঁদে শরৎশশী” হইততাহা হইলে সদানন্দের চক্ষে এত শীঘ্র এমনি করিয়া জল আসিত কি না তাহাতে বিলক্ষণ সন্দেহ। সে হয়ত বিরহ বেদনাটা ছাড়িয়া দিয়া প্রথম শরৎশশীর বাস্তব নির্ণয় করিতে বসিত। শরৎশশী রাধার বিশেষণ হইতে পারে কি না তাহা বেশ করিয়া আলোচনা করিয়া পরে অশ্রুজল সম্বন্ধে মীমাংসা করিত। কিন্তু গায়ক যদি গায়িতেন “ঘরের কোণেতে বসে কাঁদে শরৎশশী” তাহা হইলে অনুমান হয় করুণ রসের পরিবর্তে হাস্যরসেরই উদ্রেক হইত। যেন ঘরের কোণেতে বসিয়া ক্রন্দনটা ক্রন্দন নামের যোগ্য হইতে পারে নাকিংবা শরৎশশীর বিরহ হইতে নাইঅথবা হইলেও কান্নাকাটি করা তাহার পক্ষে উপযুক্ত হয় নাই। তাহা হইলে দেখা গেল যেবিরহবেদনাজনিত দুঃখই সদানন্দের অশ্রু জলের পূর্ণ হেতু নহে। তাহা যদি হইততাহা হইলে শরৎশশীর দুঃখে তাহাকে অশ্রুজল লইয়া এরূপ মারামারি করিতে হইত না।
কিন্তু রাধারই জন্য এত মাথাব্যথা কেনএকটু কারণ আছেতাহা ক্রমে বলিতেছি।
উত্তুঙ্গ হিমালয়শিখরের ধবল নগ্ন শোভা কেবল চক্ষুষ্মান অনুভব করিতে পারে—অন্ধে পারে না। অন্ধের নিকট হিমাচল শরীর সঙ্কুচিতও করে নাসম্পদশোভাও আবৃত্ত রাখে না। তথাপি অন্ধ সে সৌন্দর্য উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয় না। এ অক্ষমতার কারণ তাহার চক্ষুহীনতা। যে তাহাকে বুঝাইয়া দিবে হিমালয়শিখর কি উচ্চকি মহান্কি গম্ভীরকি সৌন্দর্যে সুশোভিতসে তাহার নাই। তাহার পর যেকেহ পর্বতের শোভা হৃদয়ে একবার অনুভব করিয়াছে সেই কেবল দুইচারিখানা শিলাখণ্ডের কৃত্রিম সন্নিবেশ দেখিয়া আনন্দউপলব্ধি করিতে পারে। যে কখন দেখে নাই সে পারে না। যে দেখিয়াছে তাহাকে এই দুই-চারিটি শিলাখণ্ডই স্মৃতি-মন্দিরের রাজদ্বার উন্মোচিত করিয়া পূর্বদৃষ্ট পর্বতের সন্নিকটে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে, অতীত জীবনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে পারে। এই সক্ষমতাই ক্ষুদ্র শিলাখণ্ডের গৌরব। সে যে শ্লাঘ্যের ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি, মহত্ত্বের ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব, প্রতিবিম্বের ইহাই শ্লাঘা—ছায়ার ইহাই মহত্ত্ব।
ভক্তের নিকট বৃন্দাবনের একবিন্দু বালুকণাও সমাদরে মস্তকে স্থান পায়, সে কি বালুকণার বস্তুগত গুণ, না বৃন্দাবনের মাহাত্ম্য? তাহারা মহতের স্মৃতি লইয়া, ভক্ত বাঞ্ছিতের ছায়াস্বরূপিণী হইয়া মর্মে উপস্থিত হয়, তাই তাহাদের এত সম্মান, এত পূজা।
সন্তানহারা জননীর নিকট তাহার মৃতশিশুর পরিত্যক্ত হস্তপদহীন একটা মৃৎ-পুত্তলিকার হয়ত বক্ষে স্থানপ্রাপ্তি ঘটে। কেন যে তুচ্ছ মৃৎপিণ্ডের এতটা গৌরব, সে কথা কি আর বুঝাইয়া দিতে হইবে? বক্ষে স্থান দিবার সময় জননী মনে করেন না যে, ইহা একটা তুচ্ছ মাটির ঢেলা। তাঁহার নিকট সে তাঁহার মৃতপুত্রের ছায়া। যদি কখন পুত্তলিকার কথা মনে হয়—সে মুহূর্তের জন্য। তাহার পর সমস্ত প্রাণমন, গত জীবন, পুত্রের স্মৃতিতে ভরিয়া উঠে। তুচ্ছ মৃৎপিণ্ডের ইহার অধিক আর কি উচ্চাশা থাকিতে পারে? সে একটি হৃদয়েও সুখ দিয়াছে ইহাই তাহার শ্লাঘা।
আর রাধার বিরহ-ব্যথায় সদানন্দের অশ্রুজল! যমুনাতীরে বসিয়া যখন বিরহবিধুরা শ্রীরাধা মর্মান্তিক যন্ত্রণায় হৃদয়ের প্রতি শিরা সঙ্কুচিত করিয়া তপ্ত অশ্রুজল বিসর্জন করিতেছিলেন, তাঁহার কি মনে হইয়াছিল কবে কোন্ ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে বসিয়া, তাঁহার দুঃখে সমদুঃখী হইয়া সদানন্দ চক্ষুজল বিসর্জন করিবে? যিনি ধ্যেয়, যিনি নিত্য উপাসিত, তাঁহারই ছায়া শ্রীরাধার হৃদয়মন অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল।
অন্যের তাহাতে স্থান হয় না, তাহাই সদানন্দের অশ্রুজলের কারণ, আকর, মূল,—কিন্তু সোপান বা পথ নহে। অগাধ সমুদ্র ঝঞ্ঝাবাতের সহিত যুদ্ধ করে, কিন্তু ঘোষণা করিয়া বেড়ায় না! শুধু ক্ষুদ্র তরঙ্গের দল তটপ্রান্তে আসিয়া ঘাতপ্রতিঘাতে পৃথিবীর বক্ষঃস্থল পর্যন্ত কম্পিত করিয়া বলিয়া যায়—“দেখ আমাদের কত প্রতাপ!” কূপের জল তাহা পারে না। সাগর-ঊর্মির ইহাই গর্ব যে সে অগাধ শক্তিশালী সমুদ্রের আশ্রিত। সূর্যের তেজ জননী বসুমতী প্রতিফলিত করেন, তাই তাঁহার রুদ্র প্রতাপ বুঝিতে পারি। আর সেই অনন্ত জ্যোতির্ময়ী বিশ্বপ্লাবনী রাধাপ্রেমের কথা বৃন্দা, ললিতা, বিশাখা, প্রভৃতি সখিবৃন্দ ব্যতীত আর কেহ জানিত না। যাহারা জানিতে পারিয়াছিল তাহারা মহৎ হইয়াছিল, যাহারা শুনিয়াছিল তাহারা ধন্য হইয়াছিল। তার পর কালক্রমে লোকে হয়ত সে কথা ভুলিয়া যাইত। একেবারে না ভুলিলেও তাহাতে এমন জীবন্ত মোহিনীশক্তি থাকিত না। এ মাধুরী যাঁহারা ধরিয়া রাখিয়াছেন, এ মহত্ত্ব, নশ্বর জগতের এ-সার বস্তু যাঁহারা পৃথিবীর ন্যায় প্রতিফলিত করিয়া জনসাধারণকে উচ্চে তুলিয়াছেন,—তাঁহারা, ঐ অজর চিরপ্রিয় বৈষ্ণব কবিগণ। সে রাধাপ্রেমের ছায়া তাঁহারা হৃদয়ে ধরিতে পারিয়াছিলেন এবং সরস প্রেমপূর্ণ সুধামাখা ছন্দোবন্ধে জগৎসমক্ষে প্রতিভাত করিয়াছিলেন।
স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর কহিয়াছেন—“এ জগতে বিশেষণের বাহুল্য”। এ কথা বড় সত্য। বিশেষণ না থাকিলে বিশেষ্যকে কে চিনিত! তাই মনে হয়, এই অমর কবিতাগুলি রাধাপ্রেমের বিশেষণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহাকে দেখিলে তাহার বিশেষ্যকে মনে পড়ে, বিশেষ্যের সেইটিই বিশেষণ, সেইটিই প্রতিবিম্ব, সেইটিই ছায়া।
যে বিরহ—শোকগাথা গাহিয়া অতীত দিবসের বৈষ্ণব-কবিগণ আপামর সকলকে উন্মত্ত করিয়াছিলেন, তাহারই একটি হস্তপদহীন পরিত্যক্ত মৃৎপুত্তলিকার মত, মৃত পুত্রের ছায়ার মত, এই ক্ষুদ্র, “যমুনা-পুলিনে বসে কাঁদে রাধা বিনোদিনী” পদটি সদানন্দের অশ্রু টানিয়া আনিতে সক্ষম হইয়াছিল। ক্ষুদ্র কবির ইহাই গৌরব,—ক্ষুদ্র কবিতার ইহাই মহত্ত্ব। ক্ষুদ্র ছায়া সদানন্দকে বশ করিতে পারিবে, কিন্তু রোহিণীকুমারের নিকটেও হয়ত যাইতে পারিবে না। তাহাতে ছায়ার অপরাধ কি?
মলিন বর্ষার দিনে আকাশের গায় নিবিড় জলদজাল বায়ুভরে চালিত হইতে দেখিলে মনে পড়ে, সেই যক্ষের কথা। মনে হয়, আজিও বুঝি তেমনি করিয়া উন্মত্ত যক্ষ ঐ মেঘপানে চাহিয়া প্রণয়িণীর সহিত কথা কহিতে চাহিতেছে। স্মরণ হয়, যেন যক্ষবধূর বিরহক্লিষ্ট ম্লান মুখশোভা কোথায় কোন্ মায়ার দেশে দেখিয়া আসিয়াছি। কিন্তু যে মনস্বী এই জীবন্ত মূর্তিময় মানসপটে গভীরভাবে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন, জলদজাল সেই মহান্ প্রতিভার ছায়ামাত্র। আপনার শরীর সেই উজ্জ্বল জ্যোতির প্রতিবিম্ব বহিয়া লইয়া বেড়ায়, মেঘের ইহাই গর্ব! তাহার আনন্দ যে, সে মহতের আশ্রিত।
তাই পূর্বে বলিতেছিলাম, সমুদ্রের জল যাহা পারে, কূপের জল তাহা পারে না। যে-দুঃখে সদানন্দ রাধার জন্য কাঁদিতে পারিয়াছিল, সে-দুঃখে হয়ত শরৎ-শশীর জন্য কাঁদিতে পারিত না। ইহাতে সদানন্দের দোষ দিই না—শরৎ-শশীর অদৃষ্টের দোষ দিই। শরৎ-শশীর দুঃখে কাঁদাইতে হইলে আর কোন মনস্বীর প্রয়োজন—ক্ষুদ্র ছায়ার কর্ম নহে। ছায়ার নিজের মহত্ত্ব কিছুই নাই, সে যখন মহতের আশ্রিত হইতে পারিবে তখনই তাহার মহত্ত্ব। হইতে পারে সে রাজপথের ধূলা, কিন্তু বৃন্দাবনের পবিত্র রজঃ হইবার আকাঙ্ক্ষা যে তাহার একেবারে দুরাশা তাহাও মনে হয় না।
কিন্তু কথায় কথায় দরিদ্র সদানন্দের কথা ভুলিয়াছি। সে-রাত্রে সে আর উঠে নাই। প্রভাত হইলে রোহিণীকুমার জানালায় আসিয়া দেখিল, সদানন্দ তেমনি মাথা নিচু করিয়া বসিয়া আছে। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভাবিল, সদানন্দ কি বসিয়া ঘুমাইতে পারে? তাহার পর ডাকিল, “সদা—ও সদানন্দ!”
সদানন্দ জাগ্রত ছিল, উত্তর দিল, “কি?”
“জেগে আছ?”
“আছি”।
“সমস্ত রাত?”
“বোধ হয়।”
রোহিণীকুমার বিস্মিত হইয়া মনে মনে ভাবিল, এ কিরূপ নেশা? তাহার পর একটু থামিয়া—একটু চিন্তা করিয়া বলিল, “সদানন্দ, মনে করিতেছি এ কু-অভ্যাসটা ছাড়িয়া দিব। তুমি শোও গে—আমি যাই। আর একদিন দেখা হবে।”
শ্রী—চট্টোপাধ্যায়।
শ্রাবণ ১৩০৮ (‘যমুনা’, মাঘ ১৩২০)*
জলধর-সম্বর্ধনা
পরম শ্রদ্ধাস্পদ—
রায় শ্রীযুক্ত জলধর সেন বাহাদুরের
করকমলে—
বরেণ্য বন্ধু,
তোমার দীর্ঘজীবনের একনিষ্ঠ সাহিত্য-সাধনায় আমাদের মানসলোকে তুমি পরমাত্মীয়ের আসন লাভ করিয়াছ।
তোমার অকলঙ্ক চরিত্র, নিষ্কলুষ অন্তর, শুভ্র সদাচার আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে, তোমার স্নেহে তোমার সৌজন্যে আমরা মুগ্ধ, আমাদের অকপট মনের ভক্তি-অর্ঘ্য তুমি গ্রহণ কর।
বাণীর মন্দিরদ্বারে তুমি সকলকে দিয়াছ অবারিত পথ, কনিষ্ঠগণকে দিয়াছ আশা,
দুর্বলকে দিয়াছ শক্তি, অখ্যাতকে দিয়াছ খ্যাতি, আত্মপ্রত্যয়হীন, শঙ্কাকুল কত আগন্তুকজনই না সাহিত্যপূজার বেদীমূলে তোমার ভরসা ও বিশ্বাসের মন্ত্রে স্বকীয় সার্থকতা খুঁজিয়া পাইয়াছে।
সাহিত্য-ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন তুমি আনন্দ বিতরণ করিতে। সে ব্রত তোমার সফল হইয়াছে। তোমার সৃষ্টি কাহাকেও আহত করে না, তোমার অন্তঃপ্রকৃতির মতোই সে সৃষ্টি স্বচ্ছন্দ সুন্দর ও অনাড়ম্বর। তোমার দুঃখ-বেদনাভরা হৃদয় একান্ত সহজেই জগতের সকল দুঃখকে আপন করিয়াছে,তাই ব্যথিত যে জন সে তোমারই সৃষ্টির মাঝে আপনার শান্তি ও সান্ত্বনার পথের সন্ধান পাইয়াছে।
হে নিরহঙ্কার বাণীর পূজারী, তুমি আজ বঙ্গের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন গ্রহণ কর। ইতি—তোমার স্বদেশবাসীর পক্ষ হইতে—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
জাগরণ – ০১
এক
ব্যারিস্টার মিস্টার আর. এম. রে ব্রাহ্ম ছিলেন না, গোঁড়া হিন্দু ত ছিলেনই না, হয়ত বা আঠারো আনা ‘বিলাত ফেরতের জাতি’ও নাও হইবেন; তবে এ কথা সত্য যে, তাঁহার পিতা-মাতা যখন আরাধ্য দেব-দেবী স্মরণ করিয়া সপ্তপুরুষের অক্ষয় স্বর্গকামনায় একমাত্র পুত্রের নাম শ্রীরাধামাধব রায় রাখিয়াছিলেন, তখন অতি বড় দুঃস্বপ্নেও তাঁহারা কল্পনা করেন নাই যে, এই ছেলে একদিন আর. এম. রে হইয়া উঠিবে, কিংবা তাহার খাদ্য অপেক্ষা অখাদ্যে এবং পরিধেয়ের পরিবর্তে অপরিধেয় বস্ত্রেই আসক্তি দুর্মদ হইয়া দাঁড়াইবে। যাই হউক, সেই পিতা-মাতারা আজ যখন জীবিত নাই এবং পরলোকে বসিয়া পুত্রের জন্য তাঁহারা মাথা খুঁড়িতেছেন কিংবা চুল ছিঁড়িতেছেন অনুমান করা কঠিন, তখন এই দিকটা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহার যে দিকটায় মতদ্বৈধের আশঙ্কা নাই, সেই দিকটাই বলি।
ইঁহার রাধামাধব অবস্থাতেই বাপ-মায়ের মৃত্যু হয়। কলেরা রোগে সাত দিনের ব্যবধানে যখন তাঁহারা মারা যান, ছেলেকে এন্ট্রান্স পাসটুকু পর্যন্ত করাইয়া যাইতে পারেন নাই। তবে এই একটা বড় কাজ করিয়া গিয়াছিলেন যে, ছেলের জন্য জমিদারি এবং বহু প্রজার রক্তজমাট-করা অসংখ্য টাকা এবং ইহার চেয়েও বড় এক অতিশয় বিশ্বাসপরায়ণ ও সুচতুর কর্মচারীর প্রতি সমস্ত ভারার্পণ করিয়া যাইবার অবকাশ এবং সৌভাগ্য তাঁহাদের ঘটিয়াছিল। কিন্তু এ-সকল অনেক দিনের কথা। আজ ‘সাহেবে’র বয়স পঞ্চাশোর্ধে গিয়াছে, দেশের সে রাজশেখর দেওয়ানও আর নাই, সে-সব দেবসেবা, অতিথিসৎকারের পালাও বহুকাল ঘুচিয়াছে। এখন ইংরাজীনবিস ম্যানেজার এবং সেই সাবেক কালের বাড়ি-ঘরের স্থানে যে ফ্যাশনের বিল্ডিং উঠিয়াছে, মালিক মিস্টার আর. এম. রে’র মত ইহাদেরও পৈতৃকের সহিত কোন জাতীয়ত্ব নাই। অথচ, এই-সকল নবপর্যায়ের সহিতও যে যথেষ্ট সম্পর্ক রাখিয়াছেন, তাহাও নয়। কেবল দূর হইতে সত্ত্ব নিংড়াইয়া যে রস বাহির হয়, তাহাই পান করিয়া এতকাল আত্ম এবং সাহেবত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন। এইখানে তাঁহার কর্মজীবনের আরও দু-একটা পরিচয় সংক্ষেপে দেওয়া আবশ্যক।
ব্যারিস্টারি পাস করিয়া বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া তাঁহারই মত আর এক ‘সাহেবে’র বিদুষী কন্যাকে বিবাহ করেন এবং যথাক্রমে অযোধ্যা, প্রয়াগ, বোম্বাই এবং পাঞ্জাবে প্র্যাক্টিস করেন। ইতিমধ্যে স্ত্রী, পুত্র এবং কন্যা লইয়া বার-তিনেক বিলাত যাতায়াত করেন এবং আর যাহা করেন, তাহা এই গল্পের সম্বন্ধে নিষ্প্রয়োজন। ছেলেটি ত ডিফ্থিরিয়া রোগে শৈশবেই মারা যায়, এবং পত্নীও দীর্ঘকাল রোগভোগের পর বছর-তিনেক হইল নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। সেই হইতে রে সাহেবেও প্র্যাক্টিস বন্ধ করিয়াছেন। ঐ ঐ স্থানগুলায় যথেষ্ট-পরিমাণ অর্থ না থাকার জন্যই হউক বা স্ত্রীর মৃত্যুতে বৈরাগ্যোদয় হওয়াতেই হউক, এক সাহেবিআনা ব্যতীত আর সমস্তই ত্যাগ করিয়া তিনি একমাত্র মেয়েটিকে লইয়া পশ্চিমের একটা বড় শহরে নির্বিঘ্নে বাস করিতেছিলেন। এমনি সময়ে একদিন তাঁহার নিশ্চিন্ত শান্তি ও সুগভীর বৈরাগ্য দুই-ই যুগপৎ আলোড়িত করিয়া মহাত্মা গান্ধীর নন্-কোঅপারেশনের প্রচণ্ড তরঙ্গ একমুহূর্তে একেবারে অভ্রভেদী হইয়া দেখা দিল। হঠাৎ মনে হইল, এই ভয়লেশহীন শুদ্ধ শান্ত সন্ন্যাসীর সুদীর্ঘ তপস্যা হইতে যে ‘অদ্রোহ অসহযোগ’ নিমিষে বাহির হইয়া আসিল, ইহার অক্ষয় গতিবেগ প্রতিরোধ করিবার কেহ নাই। যেথায় যত দুঃখ-দৈন্য, যত উৎপাত-অত্যাচার, যত লোভ ও মোহের আবর্জনা যুগ-যুগান্ত ব্যাপিয়া সঞ্চিত হইয়া আছে, ইহার কিছুই কোথাও আর অবশিষ্ট থাকিবে না, সমস্তই এই বিপুল তরঙ্গবেগে নিশ্চিহ্ন হইয়া ভাসিয়া যাইবে।
কলিকাতার মেল ক্ষণকাল পূর্বে আসিয়াছে, বাহিরের ঢাকা বারান্দায় আরামকেদারায় বসিয়া রে-সাহেব জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনের বিবরণ নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতেছিলেন, এমন সময় নীচে গাড়িবারান্দায় মোটরের শব্দ শোনা গেল এবং মিনিট-দুই পরেই তাঁহার কন্যা আলেখ্য রায় বাহিরে যাইবার পোশাকে সজ্জিত হইয়া দেখা দিলেন। মেয়েটির রঙ ফরসা নয়; কারণ, বাঙালী ‘সাহেবদের’ মেয়েরা ফরসা হয় না, কেবল সাবান ও পাউডারের জোরে চামড়াটা পাঁশুটে দেখায়। তবে দেখিতে ভাল। মুখে-চোখে দিব্য একটি বুদ্ধির শ্রী আছে, স্বাস্থ্য ও যৌবনের লাবণ্য সর্বদেহে টলটল করিতেছে, বয়স বাইশ-তেইশের বেশি নয়; কহিল—বাবা, ইন্দুর বাড়িতে আজ আমাদের টেনিস টুর্নামেন্ট, আমি যাচ্ছি। ফিরতে যদি একটু দেরি হয় ত ভেবো না।
‘সাহেব’ কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। তাঁহার চোখের দৃষ্টি উত্তেজনায় উজ্জ্বল, মুখে আবেগ ও আশঙ্কার ছায়া পড়িয়াছে, মেয়ের কথা কানেও যায় নাই। বলিয়া উঠিলেন—আলো, এই দেখ মা, কি-সব কাণ্ড! বার বার বলেছি, এ-সব হতে বাধ্য, হয়েছেও তাই।
মেয়ে বাবাকে চিনিত। তাঁহার কাছে সংসারের যাহা কিছু ঘটে, তাহাই ঘটিতে বাধ্য এবং তিনি তাহা পূর্বাহ্ণেই জানিতেন। সুতরাং এটা যে ঠিক কোন্টা, তাহা আন্দাজ করিতে না পারিয়া কহিল—কি হয়েছে বাবা?
বাবা তেমনি উদ্দীপ্ত ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিলেন—কি হয়েছে? দু’জন নন্-কো-অপারেটার ছাত্রকে ম্যাজিস্ট্রেট ধরে নিয়ে গিয়ে হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির জেল দিয়েছে, আরো পাঁচ-সাত-দশজনকে ধরবার হুকুম দিয়েছে, কি জানি, এদেরই বা কি সাজা হয়! এই বলিয়া একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া নিজেই বলিলেন—আর যা হবে, তাও জানি। খাটুনির জেল ত বটেই এবং এক বছরের নীচেও যে কেউ যাবে না, তাও বেশ বোঝা যায়। এই বলিয়া তিনি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।
আলেখ্য এ-সকল বিষয়ে মনও দিত না, এখন সময়ও ছিল না। আসন্ন টুর্নামেন্টের চিন্তাতেই সে ব্যস্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার সঙ্গীহীন, শোকজীর্ণ অকালবৃদ্ধ পিতার আগ্রহ ও আশঙ্কাকেও অবহেলা করিয়া চলিয়া যাইতে পারিল না। পাশের চেয়ারটার হাতলের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—ছেলে দু’টি কি করেছিল বাবা?
পিতা কহিলেন—তা করেছেও কম নয়। চারিদিকে গান্ধীর নন্-কোঅপারেশন মত প্রচার করে বেড়িয়েছে; দেশের লোককে ডেকে বলেছে, কেউ তোমরা মারামারি কাটাকাটি করো না, কোন ব্যক্তি-বিশেষ বা ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করো না, কিন্তু এই অনাচারী, ধর্মহীন, সত্যভ্রষ্ট বিদেশী গভর্নমেন্টের সঙ্গেও আর কোন সম্পর্ক রেখো না, চাকরির লোভে এর দ্বারে যেয়ো না, বিদ্যের জন্যে এর স্কুল-কলেজে ঢুকো না, বিচারের আশায় আদালতের ছায়া পর্যন্ত মাড়িও না।
আলেখ্য কহিল—তার মানে, সমস্ত দেশটাকে এরা আর একবার মগের মুল্লুক বানিয়ে তুলতে চায়।
রে বলিলেন—তা ছাড়া আর কি যে হতে পারে, আমি ত ভেবে পাইনে!
আলেখ্য কহিল—তাহলে এদের জেলে যাওয়াই উচিত। বাস্তবিক, মিছামিছি সমস্ত দেশটাকে যেন তোলপাড় করে তুলেছে।
মেয়ের কথায় পিতা পূর্ণ সম্মতি দিতে পারিলেন না। একটু দ্বিধা করিয়া বলিলেন,—না, ঠিক যে মিছামিছি করছে তাও নয়, গভর্নমেন্টেরও অন্যায় আছে।
আলেখ্য গভর্নমেন্টের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কিছুই প্রায় জানিত না। খবরের কাগজ পড়িতে তাহার একেবারে ভাল লাগিত না, দেশ বা বিদেশের কোথায় কি ঘটিতেছে, না ঘটিতেছে, এ লইয়া নিজেকে নিরর্থক উদ্বিগ্ন করিয়া তোলার সে কোন প্রয়োজন অনুভব করিত না। সুমুখের ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, তখনও তাহার মিনিট-দশেক সময় আছে, বাবাকে একলা ফেলিয়া যাইবার পূর্বে কোন কিছু একটা অছিলায় এই স্বল্পকালটুকুও তাঁহাকে সঞ্জীবিত ও সচেতন করিয়া যাইবার লোভে কহিল—বাবা, মুখে তুমি যাই কেন না বল, ভেতরে ভেতরে কিন্তু তুমি এই সব লোকেদেরই ভালোবাসো। এই যে সেদিন হরতালের দিন ইন্দুদের মোটরের উইন্ডস্ক্রীনটা ইঁট মেরে ভেঙ্গে দিলে, তুমি শুনে বললে, এ-রকম একটা বড় ব্যাপারে ও-সব ছোটখাটো অত্যাচার ঘটেই থাকে। গাড়িতে ইন্দুর বাবা ছিলেন, ধর, যদি ইঁটটা তাঁর গায়েই লাগতো?
কন্যার অভিযোগে পিতা একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—না না, আমাকে তুমি ভুল বুঝেছ আলো। এই সব দুরন্তপনা আমি মোটেই পছন্দ করিনে এবং যারা করে তাদের শাস্তি দিতেই বলি। কিন্তু তাও বলি, মিস্টার ঘোষের সেদিন গাড়িতে না বার হওয়াই উচিত ছিল। দেশে এতগুলো লোকের সনির্বন্ধ অনুরোধ উপেক্ষা করাই কি ভাল মা?
আলেখ্য রাগ করিয়া কহিল—অনুরোধ করলেই হল বাবা? বরঞ্চ, আমি ত বলি, অন্যায় অনুরোধ যেদিক থেকেই আসুক, তাকে অগ্রাহ্য করাই যথার্থ সাহস। এ সাহস তাঁর ছিল বলে তাঁকে বরঞ্চ ধন্যবাদ দেওয়াই উচিত।
রে-সাহেব সামান্য একটুখানি উত্তেজনার সহিত প্রশ্ন করিলেন—এ অনুরোধ অন্যায়, এ তুমি কি করে বুঝলে আলো?
আলেখ্য কহিল—তাঁর নিজের গাড়িতে চড়বার তাঁর সম্পূর্ণ অধিকার আছে। নিষেধ করাই অন্যায়।
তাহার পিতা বলিলেন—এটা অত্যন্ত মোটা কথা মা।
কন্যা কহিল—মোটা কথাই বাবা, এবং এই মোটা কথা মেনে চলবার বুদ্ধি এবং সাহসই যেন সংসারে বেশী লোকের থাকে।
সেদিন গাড়ির এই কাঁচভাঙ্গা লইয়া ইন্দুদের বাটীতে যে-সকল তীক্ষ্ণ ও কঠিন আলোচনা হইয়াছিল, সে-সকল আলেখ্যের মনে ছিল, তাহারই সূত্র ধরিয়া কণ্ঠস্বর তাহার উত্তপ্ত হইয়া উঠিল; কহিল, তিনি কিছুই অন্যায় করেন নি, বরঞ্চ যে-সব ভীতু লোক ভয়ে ভয়ে এই-সব স্বদেশী গুণ্ডাদের প্রশ্রয় দিয়েছিল, তারাই ঢের বেশী অন্যায় করেছিল বাবা, এ তোমাকে আমি নিশ্চয় বলছি।
সাহেবের মুখ মলিন হইল। কিন্তু আলেখ্যেরও চক্ষের পলকে মনে পড়িল, তাঁহার পিতা অসুস্থ শরীরেও সেদিন সকালে পায়ে হাঁটিয়া ডাক্তারখানায় গিয়েছিলেন এবং ডাক্তারের বারংবার আহ্বান সত্ত্বেও তেমনি হাঁটিয়াই বাটী ফিরিয়াছিলেন। পাছে তাহার তীক্ষ্ণ মন্তব্য ঘুণাগ্রেও পিতার কার্যের সমালোচনার মত শুনাইয়া থাকে, এই লজ্জায় সে একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল। তাহার ভগ্নস্বাস্থ্য দুর্বলচিত্ত পিতাকে সে ভাল করিয়াই জানিত। দেহের ও মনের কোনদিন কোন তেজ ছিল না বলিয়া তিনি সংসারে সকল সুবিধা পাইয়াও কখনও উন্নতি করিতে পারেন নাই। শত্রু-মিত্র অনেকের কাছে, বিশেষ করিয়া নিজের স্ত্রীর কাছে অনেকদিন অনেক কথাই এই লইয়া তাঁহাকে শুনিতে হইয়াছে, ফলোদয় কিছুই হয় নাই। এমনি ভাবেই সারা জীবন কাটিয়াছে,—কিন্তু সেই জীবনের আজ অপর প্রান্তে পৌঁছিয়া মেয়ের মুখ হইতে সেই সকল পুরানো তিরস্কারের পুনরাবৃত্তি শুনিলে দুঃখের আর বাকি কিছু থাকে না।
আলেখ্য তাড়াতাড়ি পিতার কাছে আসিয়া তাঁহার কাঁধের উপর একটা হাত রাখিয়া আদর করিয়া কহিল—কিন্তু তাই বলে তুমি যেন ভেবো না বাবা, তোমার কোন কাজকে আমি অন্যায় মনে করি।
পিতা একটু আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আমার কোন্ কাজ মা? সেদিনকার নিজের কথা তাঁহার মনেও ছিল না।
মেয়ে বাপের মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল—কোন কাজই নয় বাবা, কোন কাজই নয়। অন্যায় তুমি যে কিছু করতেই পারো না। তবুও তোমাকে যারা সেদিন অসুখ শরীরে ডাক্তারখানায় হেঁটে যেতে-আসতে বাধ্য করলে, বল ত বাবা, তারা কতখানি অন্যায় অত্যাচার করেছিল।
সাহেবের ঘটনাটা মনে পড়িল। তিনি সস্নেহে মেয়ের মাথার উপর ধীরে ধীরে হাত চাপড়াইতে চাপড়াইতে বলিলেন—ওঃ, তাই বুঝি তাদের ওপর তোর রাগ আলো?
এই পিতাটিকে ভুলাইতে আলেখ্যের কষ্ট পাইতে হইত না। সে কৃত্রিম ক্রোধের স্বরে কহিল—রাগ হয় না বাবা?
বাবা হাসিয়া বলিলেন—না মা, রাগ হওয়া উচিত নয়, বরঞ্চ সে আমার বেশ ভালই লেগেছিল। ছোট-বড় উঁচু-নিচু নেই, সবাই পায়ে হেঁটে চলেছে, পা যে ভগবান দিয়েছেন, তার ব্যবহারে যে লজ্জা নেই, এ কথা সেদিন যেমন অনুভব করেছিলাম মা, এমন আর কোনদিন নয়। বহুকাল এ কথা আমার মনে থাকবে আলো।
ইহা যে কোন যুক্তি নয়, আলেখ্য তাহা মনে মনে বুঝিল, তথাপি এই লইয়া আর নূতন তর্কের সৃষ্টি করিল না। ঘড়িতে পাঁচটা বাজিতেই কহিল—চল না বাবা, আজ আমাদের টুর্নামেন্ট দেখতে যাবে। ইন্দুর মা যে কত খুশী হবেন, তা আর বলতে পারিনে।
পিতাকে কোনকালেই সহজে বাটীর বাহির করা যাইত না, বিশেষ করিয়া তাহার মায়ের মৃত্যুর পর। ঘর এবং এই ঢাকা বারান্দাটি ধীরে ধীরে তাঁহার কাছে সমস্ত পৃথিবীতে পরিণত হইতেছিল। জড়তায় দেহ ক্রমশ: ভাঙ্গিয়া আসিতেছিল, কিন্তু কোথাও বাহির হইবার প্রস্তাবেই তাঁহার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইত। মেয়ের কথায় ভয় পাইয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন—এখন? এই অসময়ে?
মেয়ে হাসিয়া বলিল—এই ত বেড়াতে যাবার সময় বাবা।
কিন্তু আমার যে বিস্তর চিঠি লেখবার রয়েছে আলো! তুমি বরঞ্চ একটু শীঘ্র শীঘ্র ফিরো, যেন অধিক রাত না হয়, আমি ততক্ষণ হাতের কাজগুলো সেরে ফেলি। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সংবাদপত্রে মনঃসংযোগ করিলেন।
এই মেয়েটির ক্ষুদ্র জীবনের একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এইখানে দেওয়া প্রয়োজন। আলেখ্য নামটি মা রাখিয়াছিলেন বোধ করি নূতনত্বের প্রলোভনে। হয়ত এমন অভিসন্ধিও তাঁহার মনে গোপনে ছিল, হিন্দুদের কোন দেবদেবীর সহিতই না ইহার লেশমাত্র সাদৃশ্য কেহ খুঁজিয়া পায়; কিন্তু পিতা প্রথম হইতেই নামটা পছন্দ করেন নাই, সহজে উচ্চারণ করিতেও একটু বাধিত, তাই মেয়েকে তিনি ছোট করিয়া আলো বলিয়াই ডাকিতেন। এই সোজা নামটাই তাহার ক্রমশ: চারিদিকে প্রচলিত হইয়া গিয়াছিল। ইন্দুদের সহিত তাহার পরিচয় ছেলেবেলার। ইন্দুর মা ও তাহার মা স্কুলে একত্রে পড়িয়াছিলেন, কিছুকাল এক বোর্ডিঙে বাস করিয়াছিলেন এবং আমরণ অতিশয় বন্ধু ছিলেন।
ইন্দুর দাদা কমলকিরণ যখন বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়িতে যায়, তখন এই শর্তই হইয়াছিল যে, সে পাস করিয়া ফিরিলে তাহারই হাতে কন্যা সম্প্রদান করিবেন। বছর-খানেক হইল কমলকিরণ পাস করিয়া কে. কে. ঘোষ হইয়া দেশে ফিরিয়াছে, তাহার পিতা-মাতা মৃত-পত্নীর প্রতিশ্রুতিও বার-কয়েক রে সাহেবের গোচর করিয়াছেন, কিন্তু এমনি দুর্বলচিত্ত তিনি যে, হাঁ কিংবা না, কোনটাই অদ্যাবধি মনস্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ইন্দুদের বাটীতে টুর্নামেন্ট দেখিবার নিমন্ত্রণমাত্রই কেন যে তিনি অমন করিয়া আপনাকে খবরের কাগজের মধ্যে নিমগ্ন করিয়া ফেলিলেন, ইহার যথার্থ হেতু মেয়ে যাহাই বুঝুক, ইন্দুর মা শুনিলে তাহার অন্যপ্রকার অর্থ করিতেন। তথাপি আলেখ্যকে বধূ করিবার চেষ্টা হইতে তিনি এখনও বিরত হন নাই। তাহার মত মেয়ে রূপে গুণে দুর্লভ নয় তিনি জানিতেন, কিন্তু রোগগ্রস্ত পিতার মৃত্যুর পরে যে সম্পত্তি তাহার হস্তগত হইবে, তাহা যে সত্যই দুর্লভ, ইহাও তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন। অন্যপক্ষে পাত্র হিসাবে কমলকিরণ অবহেলার সামগ্রী নহে। সে শিক্ষিত রূপবান; পিতার জুনিয়ারি করিতেছে,—ভবিষ্যৎ তাহার উজ্জ্বল। মা কথা দিয়াছিলেন, আলেখ্য তাহা জানিত। ইন্দু ও তাহার জননী যখন-তখন তাহা শুনাইতেও ত্রুটি করিতেন না। সকলেই প্রায় একপ্রকার নিশ্চিত ছিলেন যে, অল্পবুদ্ধি বৃদ্ধের মনস্থির করিতে বিলম্ব হইতে পারে, কিন্তু স্থির যখন একদিন করিতেই হইবে, তখন এদিকে আর নড়চড় হইবে না। প্রমাণস্বরূপে তিনি আলেখ্যের সুমুখেই তাঁহার স্বামীকে বলিতেন, সন্দেহ করবার আমি ত কোন কারণ দেখিনে। অমত থাকলে মিঃ রে কখনও আলোকে এমন একলা আমাদের বাড়ি পাঠাতেন না। মনে মনে তিনি খুব জানেন, তাঁর মেয়ে আপনার বাড়িতে আপনার লোকজনের কাছেই যাচ্ছে। কি বলো মা আলো? কমল উপস্থিত থাকিলে মুখ তাহার রাঙ্গা হইয়া উঠিত। পুরুষেরা না থাকিলে সে সহজেই সায় দিয়া সলজ্জকণ্ঠে কহিত—বাবা ত সত্যিই জানেন, আপনি আমার মায়ের মত।
এই একটা বছর এমনিভাবেই কাটিয়া গিয়াছিল।
টেনিস টুর্নামেন্টের অদ্যকার পালা সমাপ্ত হইলে ইন্দুদের বাটীতে চা ও সামান্য কিছু জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। সে-সকল শেষ হইতে সন্ধ্যা বহুক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু সেদিকে আলেখ্যের আজ খেয়ালই ছিল না।
সে ভাল খেলিত, কানপুর হইতে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা হারিয়া গিয়াছিলেন, সেই জয়ের আনন্দে মন তাহার আজ অত্যন্ত প্রসন্ন ছিল। তথাপি ইন্দুর গান শেষ না হইতেই তাহাকে ঘড়ির দিকে চাহিয়া অলক্ষ্যে উঠিয়া পড়িতে হইল এবং সঙ্গীহীন পিতার কথা স্মরণ করিয়া বিদায়গ্রহণের প্রচলিত আচরণটুকু পরিহার করিয়াই তাহাকে দ্রুতপদে নীচে নামিয়া আসিতে হইল। মোটর তাহার প্রস্তুত ছিল, শোফার দ্বার খুলিয়া দিতেই গাড়িতে উঠিয়া পরিশ্রান্ত দেহলতা সে এলাইয়া দিয়া বসিল। রাত্রি অন্ধকার নহে, আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, অদূরে একটা বিলাতী লতার কুঞ্জ হইতে একপ্রকার উগ্র গন্ধে নিঃশ্বাসের বাতাস যেন ভারী হইয়া উঠিয়াছে। অত্যধিক খেলার পরিশ্রমে সে ক্লান্ত, কিন্তু যৌবনের উষ্ণ রক্ত তখনও খরবেগে শিরার মধ্যে বহিতেছে—এমন না বলিয়া চুপি চুপি আসাটা ভাল হইল না, সে ভাবিতেছে, এমন সময়ে ঠিক কানের কাছে শুনিল, হঠাৎ পালিয়ে এলে যে আলো?
আলেখ্য চকিত হইয়া উঠিয়া বসিয়া কহিল,—এঁরা কিছু বলছেন বুঝি?
কমল হাসিয়া কহিল—না। তার কারণ, আমি ছাড়া আর কেউ জানতেই পারেন নি। কিন্তু আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া শক্ত। জ্যোৎস্নার আলোকে আলেখ্যের মুখের চেহারা দেখা গেল না। সে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কহিল—আপনি ত জানেন, বাবা একলা আছেন, একটু রাত হলেই তিনি বড় ব্যস্ত হন।
কমল ঘাড় নাড়িয়া বলিল—জানি এবং সেই জন্যে রাত করা তোমার উচিতই নয়।
শোফার গাড়িকে প্রস্তুত করিয়া উঠিয়া বসিতেই কমল চুপি চুপি বলিল—হুকুম দাও ত তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।
আলেখ্য মনে মনে লজ্জা বোধ করিল, কিন্তু না বলিতে পারিল না। শুধু জিজ্ঞাসা করিল, আপনি ফিরবেন কি করে?
কমল কহিল—চমৎকার রাত, দিব্যি বেড়াতে বেড়াতে ফিরে আসবো। তখন পর্যন্ত হয়ত এঁরা কেউ টেরও পাবেন না। এই বলিয়া সে নিজেই দরজা খুলিয়া আলেখ্যের পাশে আসিয়া উপবেশন করিল।
বেশী দূর নয়, মিনিট পাঁচ-ছয় মাত্র। অতি প্রয়োজনীয় কথার জন্য ইহাই পর্যাপ্ত। কিন্তু কোন কথাই হইল না, পাশাপাশি উভয়ে চুপ করিয়া বসিয়া। গাড়ি রে-সাহেবের ফটকে আসিয়া প্রবেশ করিল। আলেখ্যের অত্যন্ত লজ্জা করিতেছিল, মোটরের শব্দে বাবা নিশ্চয়ই বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইবেন, কিন্তু উপরের বারান্দা শূন্য, কোথাও কেহ নাই।
দু’জনে অবতরণ করিলে শোফার গাড়ি লইয়া প্রস্থান করিল। কমল মৃদুকণ্ঠে বিদায় লইয়া ফিরিল, হলে ঢুকিয়া আলেখ্য বেহারাকে সভয়ে প্রশ্ন করিল—সাহেব কোথায়?
সে সেলাম করিয়া জানাইল, তিনি উপরের ঘরেই আছেন।
আলেখ্য দ্রুতপদে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া তাহার পিতার ঘরে ঢুকিয়া একেবারে আশ্চর্য হইয়া গেল। আলমারি খোলা, ঘরময় জিনিসপত্র ছড়ানো, সাহেব নিজে আর একটা বেহারাকে দিয়া বড় বড় দুটো তোরঙ্গ ভর্তি করিতেছেন।
এ কি বাবা, কোথাও যাবে নাকি?
সাহেব চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—দেখ্ দিকি সব কাণ্ড! তখন বলেছি, গান্ধী সর্বনাশ করবে! এই সব স্বদেশী গুণ্ডারা দেশটাকে লণ্ডভণ্ড করে তবে ছাড়বে, এ যে আমি শুরুতেই দেখতে পেয়েছি! এই বলিয়া তিনি পকেট হইতে একটা চিঠি লইয়া মেয়ের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলেন। বলিলেন, এদের সবাইকে ধরে জেলে না পাঠালে যে সমস্ত দেশ অরাজক হতে বাধ্য।
মাত্র ঘণ্টা তিন-চার পূর্বেই যে তিনি প্রায় উলটা কথা বলিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করাইয়া কোন লাভ নাই। আলেখ্য নিঃশব্দে চিঠিখানা তুলিয়া লইয়া আলোর সম্মুখে গিয়া এক নিঃশ্বাসে তাহা পড়িয়া ফেলিল। চিঠি তাঁহার ম্যানেজারের। তিনি দুঃখ করিয়া, বরঞ্চ কতকটা ক্রোধের সহিতই জানাইতেছেন যে, জমিদারির অবস্থা অতিশয় বিশৃঙ্খল। তিনি উপর্যুপরি কয়েকখানা পত্রে সকল বৃত্তান্ত সবিস্তারে নিবেদন করিয়াও প্রতিবিধানের কোন আদেশ পান নাই। অপিচ, প্রকারান্তরে তাহাদের প্রশ্রয় দেওয়াই হইয়াছে। দুর্বৃত্তরা ক্রমশ: এরূপ স্পর্ধিত হইয়া উঠিয়াছে যে, তাঁহাকেই অপমান করিয়াছে। এমন কি, তিনি লোকজন লইয়া স্বয়ং উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও অমরপুরের হাটে বিলাতী বস্ত্র বিক্রয় একপ্রকার বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তাহাতে জমিদারির আয় অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। অবশেষে নিরুপায় হইয়াই তিনি সকল ঘটনা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের গোচর করায় ইহাদের প্ররোচনায় বিদ্রোহী প্রজারা ধর্মঘট করিয়া খাজনা আদায় বন্ধ করিয়াছে। এমন কি, লুটপাটের ভয়ও দেখাইতেছে। সরকারী খাজনা জমা দিবার সময় হইয়া আসিল, কিন্তু তহবিলে কিছুমাত্র টাকা মজুদ নাই। ইহার আশু প্রতিকার প্রয়োজন। জনরব এইরূপ যে, মালিক নিজে না আসিলে কোন উপায় হইবে না।
চিঠি পড়িয়া আলেখ্যের মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল। রুদ্ধকণ্ঠে বলিল—বাবা, তুমি নিজে যাচ্ছো?
বাবা বলিলেন—নিজে না গেলে কি হয় মা? যাবো আর আসবো !—একটা দিনে সমস্ত শায়েস্তা হয়ে যাবে। ঘোষ-সাহেবকে বলে যাবো, তিনি দু’বেলা এসে দেখবেন, তোমার কোন কষ্ট হবে না।
মেয়ে সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল—ম্যানেজারবাবু তোমাকে বারবার সতর্ক করেছেন, তবু তুমি কিছুই করোনি বাবা?
সাহেব সতেজে বলিলেন—করেছি বৈ কি, নিশ্চয় করেছি। বোধ হয়, চিঠির জবাবও দিয়েছি।
মেয়ে ক্ষণকাল বাপের মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল—বোধ হয় দাওনি বাবা, তুমি ভুলে গেছ।
সাহেবের গলার সুর সহসা নীচের পর্দায় নামিয়া আসিল,—কহিলেন—ভুলে যাবো কেন? এই যে সেদিন নিজের হাতে লিখে দিলাম, লোকেরা বিলিতী কাপড় যদি পরতে না চায় ত হাটে এনে কাজ নেই। তাতে লোকসান ছাড়া ত লাভ নেই কারো—
তাঁহার কথা শেষ না হইতেই আলেখ্য ভীতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল—এ চিঠি আবার তুমি কাকে লিখলে বাবা? কৈ, ম্যানেজারবাবুর পত্রে ত এর কোন কথা নেই।
সাহেব চিন্তিত মুখে বলিলেন—ঐ যে সব কারা কলকাতা থেকে এসে গ্রামে গ্রামে নাইট ইস্কুল খুলেছে। চাষাভুষোদের সব মত জেনে আমার হুকুম চেয়েছিল,—তা বেশ ত, তারা যে ইচ্ছে করুক না, আমার কি? আমার খাজনা পেলেই হ’ল।
মেয়ে জিজ্ঞাসা করিল—তা হলে আমাদের গ্রামেও নাইট ইস্কুল খোলা হয়েছে?
বাবা সগর্বে বললেন—নিশ্চয় হয়েছে ! নিশ্চয় হয়েছে। আমিই ত বলে দিলাম, মন্দিরের নাটবাংলাটা পড়ে আছে, ইচ্ছে হয় তাতেই করুক। সামান্য একটু তেলের খরচা বৈ ত না।
মেয়ে কহিল—তেলের খরচও বোধ হয় কাছারি থেকেই দেওয়া হচ্ছে?
বাবা বলিলেন—হুকুম ত দিয়েছি, এখন না যদি করে, দূর থেকে আর কত দেখি বল?
মেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিল—বাবা, তুমি ও-ঘরে গিয়ে ব’সগে, আমি নিজে সব গুছিয়ে নিচ্ছি। তোমার সঙ্গে আমিও যাবো।
পিতা সবিস্ময়ে কহিলেন—তুমি যাবে?
আলেখ্য বলিল,—হাঁ বাবা—আমার বোধ হয়, আমি না গেলে চলবে না।
জাগরণ – ০২
দুই
পিতার সঙ্গে আলেখ্য জীবনে এই প্রথম তাহার স্বর্গীয় পিতামহগণের পল্লীবাসভবনে আসিয়া উপস্থিত হইল। বয়স তাহার বেশী নয়, তথাপি এই বয়সেই সে তিনবার য়ুরোপ ঘুরিয়া আসিয়াছে। দার্জিলিং ও সিমলার পাহাড় বোধ করি কোন বৎসরেই বাদ পড়ে নাই; চা ও ডিনারের অসংখ্য নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছে এবং মা বাঁচিয়া থাকিতে নিজেদের বাটীতেও তাহার ত্রুটিহীন বহু আয়োজনে যোগ দিয়াছে। গান-বাজনার মজলিস হইতে শুরু করিয়া খেলাধূলা ও সাধারণ সভা-সমিতিতে কিভাবে চলাফেরা করিতে হয়, সোসাইটিতে কেমন করিয়া কথাবার্তা কহিতে হয়, কোথায়, কবে এবং কোন্ সময়ে কি পোশাক পরিতে হয়, কোন রং, কোন্ ফুল কখন কাহাকে মানায়, এ-সকল ব্যাপার সে নির্ভুলভাবে শিক্ষা করিয়াছে; রুচি ও ফ্যাশন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার বাকি কিছু আর তাহার নাই, শুধু কেবল এই খবরটাই সে এতকাল লয় নাই, এ-সকল কোথা হইতে এবং কেমন করিয়া আসে। মা ও মেয়ে এতদিন শুধু এতটুকু মাত্র জানিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন যে, বাংলাদেশের কোন্ এক পাড়াগাঁয়ে তাহাদের কল্পবৃক্ষ আছে, তাহার মূলে জলসেক করিতে হয় না, খবরদারি লইতে হয় না, শুধু তাহাতে সময়ে ও অসময়ে নাড়া দিলেই সোনা ও রূপো ঝরিয়া পড়ে। জননী ত কোনদিনই গ্রাহ্য করেন নাই, কিন্তু আলেখ্য কখন কখন যেন লক্ষ্য করিয়াছে, এই বিপুল অপব্যয়ের যোগান দিতে পিতা যেন মাঝে মাঝে কেমন একপ্রকার বিরস ম্লান ও অবসন্ন হইয়া পড়িতেন। তাহাকে এমন আভাস দিতেও সে দেখিয়াছে বলিয়াই মনে পড়ে, যেন এতখানি বাড়াবাড়ি না হইলেই হয় ভাল। অথচ প্রত্যুত্তরে মায়ের মুখে কেবল এই কথাই সে শুনিয়া আসিয়াছে যে, সমাজে থাকিতে গেলে ইহা না করিলেই নয়। শুধু অসভ্যদের মত বনে-জঙ্গলে বাস করিলেই কোন খরচ করিতে হয় না।
পিতাকে প্রতিবাদ করিতে কখন দেখে নাই,—কিন্তু চুপ করিয়া এমন নির্জীবের মত বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছে যে, ধুমধামের মাঝখানে গৃহকর্তার সে আচরণ একেবারেই বিসদৃশ। কিন্তু সে ত ক্ষণিকের ব্যাপার, ক্ষণকাল পরে সে ভাব হয়ত আর তাঁহাতে থাকিত না।
বিশেষতঃ তখনও কত আয়োজন, কত কাজ বাকী,—নিমন্ত্রিতগণের বাড়ি ও মোটর আসিবার মুহূর্ত আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে—সে লইয়া মাথাব্যথা করিবার সময় ছিলই বা কৈ? এমনি করিয়াই এই মেয়েটির ছেলেবেলা হইতেই এতকাল কাটিয়াছে এবং ভবিষ্যতের দিনগুলাও এমনিভাবেই কাটিবার মত করিয়াই মা তাহার শিক্ষা-দীক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন।
দিন-চারেক হইল, তাঁহারা এখানে আসিয়াছেন। জমিদারের বাড়ি, বড়লোকের বাড়ি,—বড়লোকের জন্যই নূতন করিয়া নির্মিত হইয়াছিল, কোথাও কোন ত্রুটি নাই, তথাপি কত অভাব, কত অসুবিধাই না আলেখ্যের চোখে পড়িতেছে। বসিবার ঘর, খাবার ঘর, শোবার ঘরগুলার আগাগোড়া পেণ্টিং নূতন করিয়া না করাইলে ত একটা দিনও আর বাস করা চলে না। দরজা-জানালার কদর্য রং বদল না করিলেই নয়। আসবাবগুলা মান্ধাতার কালের, না আছে ছাঁদ, না আছে তাহার শ্রী, ধূলায় ধূলায় বার্নিশ ত না থাকার মধ্যেই, সুতরাং এ বাটীতে থাকিতে হইলে এ সকলের প্রতি চোখ বুজিয়া থাকা অসম্ভব। যেমন করিয়া হউক, চার-পাঁচ হাজার টাকার কমে হইবে না। এই প্রস্তাব লইয়া সেদিন সকালে আলেখ্য তাহার পিতার দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবা একজন অল্পবয়সী অধ্যাপক ব্রাহ্মণের সহিত বসিয়া গল্প করিতেছিলেন, মেয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিতে কহিলেন,—ইনি আমাদের পুরোহিত বংশের দৌহিত্র, অমরনাথ ন্যায়রত্ন, আমাদের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত বরাট গ্রামে এঁর পৈতৃক টোলে অধ্যাপনা শুরু করেছেন,—ইনি আমার কন্যা আলেখ্য রায়,—মা, এঁকে প্রণাম কর।
আদেশ শুনিয়া আলেখ্যের গা জ্বলিয়া গেল। একে ত একান্ত গুরুজন ব্যতীত ভূমিষ্ঠ প্রণাম করার রীতি তাহাদের সমাজে নাই বলিলেই হয়, তাহাতে আবার এই অপরিচিত লোকটি পুরোহিত-বংশের। এই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সে শিশুকাল হইতে সংখ্যাতীত অভিযোগ শুনিয়া আসিয়াছে; ইহাদের অন্ধতা ও অজ্ঞতা ও নিরতিশয় সঙ্কীর্ণতাই যে দেশের সকল অনিষ্টের মূল, ইহাদের প্রতিকূলতার জন্যই যে তাহারা হিন্দু-সমাজে স্থান পায় না, সেই বিশ্বাসই তাহার মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া আছে, এখন তাহাদেরই একজন অজানা ব্যক্তির পদতলে কিছুতেই তাহার মাথা হেঁট হইতে চাহিল না। সে হাত তুলিয়া ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া কোনমতে তাহার পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিল।
কিন্তু এতটুকু তাহার চক্ষু এড়াইল না যে, সে ব্যক্তি নমস্কার তাহার ফিরাইয়া দিল না, শুধু নীরবে একদৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। আলেখ্য পলকমাত্র তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিল। সে পিতার সঙ্গেই কথা কহিতে আসিয়াছিল,—সুতরাং যে অপরিচিত, তাহাকে অপরিচিতের মতই সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া দিয়া তাঁহার সঙ্গেই কথা কহিতে নিরত হইল, তথাপি সকল সময়েই সে যেন অনুভব করিতে লাগিল, এই অপরিচিত অধ্যাপকের অভদ্র বিস্মিত দৃষ্টি তাহাকে পিছন হইতে যেন নিঃশব্দে আঘাত করিতেছে।
আলেখ্য কহিল—বাবা, ঘরগুলো সব কি হয়ে আছে, তুমি দেখেছ?
পিতা কিছু আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—কেন মা, বেশ ভালই ত আছে।
কন্যা ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিল। কহিল—ওকে তুমি ভাল বল বাবা? বিশেষ করে বসবার আর খাবার ঘর দুটো? আমার ত মনে হয়, তাড়াতাড়ি একবার পেণ্ট করিয়ে না দিলে ওতে না-বসা, না-খাওয়া কোনটাই চলবে না। আচ্ছা, লোকগুলো তোমার এতদিন করছিল কি? আমার মতে এদের সব জবাব দেওয়া দরকার। পুরানো লোক দিয়ে হয় না,—তারা শুধু ফাঁকিই দেয়।
পিতা মাথা নাড়িয়া সায় দিলেন, কিন্তু আস্তে আস্তে বলিলেন—সে ঠিক কথাই বটে, কিন্তু হলোও ত অনেকদিন মা,—বাস না করলেও ঘরদোরের শ্রী থাকে না।
আলেখ্য কহিল—সে শ্রী অন্যরকমের, নইলে এ কেবল তাদের অযত্নে অবহেলায় নষ্ট হয়েছে। আমি ম্যানেজার থেকে চাকর মালী পর্যন্ত সকলের কৈফিয়ত নেবো। দোষ পেলেই শাস্তি দেবো, বাবা, তুমি কিন্তু তাতে বাধা দিতে পারবে না।
পিতা হাসিয়া কহিলেন—বাধা দিতে যাব কেন মা, সমস্তই ত তোমার। তোমার ভৃত্যদের তুমি শাসন করবে, আমি কেন নিষেধ করব? বেশ জানি, অন্যায় তুমি কারও ‘পরেই করবে না।
কন্যা মনে মনে খুশী হইল। কহিল—ফার্নিচারগুলোর দশা এমন হয়েছে যে, সেগুলো ফেলে দিলেই হয়। চার-পাঁচ হাজার টাকার কমে বোধ করি কিছুই করতে পারা যাবে না।
—এত টাকা? বৃদ্ধ শঙ্কিত হইয়া কহিলেন—কিন্তু এ জঙ্গলে তুমি ত থাকতে পারবে না আলো, দু’দিনের জন্যে খরচ করে সমস্তই আবার এমনি ধারা নষ্ট হয়ে যাবে।
আলেখ্য মাথা নাড়িল। কহিল—আমি স্থির করেছি বাবা, এবার আমরা থাকবো। যদি যেতেও হয়, বছরে অন্তত: দু’বার করে আমরা বাড়িতে আসবই। চোখ না রাখলে সমস্তই নষ্ট হয়ে যাবে, এ আমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছি।
পিতা প্রফুল্লমুখে বারবার মাথা নাড়িয়া বলিলেন—এতকাল পরে এ কথা যদি বুঝে থাক আলো, তার চেয়ে সুখের কথা আর কি আছে?—এই বলিয়া অধ্যাপকটিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—কি বল অমরনাথ, এতদিনে মেয়ে যদি এ কথা বুঝে থাকেন, তার চেয়ে আনন্দের কথা কি আছে?
অধ্যাপক হাঁ না কোন মন্তব্যই প্রকাশ করিলেন না, কিন্তু কন্যা হাসিয়া কহিল—আমার বুঝতে ত খুব বেশীদিন লাগেনি বাবা, লাগলো তোমার। বছর দশ-পনর আগেও যদি বুঝতে, আজ আমাকে আবার সমস্ত নূতন করে করতে হ’ত না।
কন্যার ইচ্ছাকে বাধা দিবার শক্তি বৃদ্ধের ছিল না। কিন্তু তাঁর মুখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা গেল, তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছেন। কহিলেন—যদি করতেও হয়, তার তাড়াতাড়ি কি? ধীরেসুস্থে করলেও ত চলবে।
মেয়ে ঘাড় নাড়িয়া বলিল—না বাবা, সে হয় না। এই বলিয়া সে তাহার হাতের একখানা ইংরাজি উপন্যাসের পাতার ভিতর হইতে খুঁজিয়া একখানা টেলিগ্রাম পিতার হাতে তুলিয়া দিল। তিনি পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া কাগজখানি আদ্যোপান্ত বার দুই-তিন পাঠ করিয়া, কন্যাকে ফিরাইয়া দিয়া ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—তাই ত ! কমলকিরণ তাঁর মা ও ভগিনীকে নিয়ে কলকাতায় আসছেন, সম্ভবত: ঘোষ-সাহেবও আসতে পারেন। কি নাগাত তাঁরা এ বাড়িতে আসবেন, কিছু জানিয়েছেন?
মেয়ে কহিল—কলকাতায় এসে বোধ হয় জানাবেন।
রে-সাহেব চশমা খুলিয়া খাপে পুরিয়া পকেটে রাখিলেন, সমস্ত মাথাজোড়া টাকের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে শুধু বলিলেন—তাই ত—
তাহার অকালবৃদ্ধ পিতার অসচ্ছলতার পরিমাণ ঠিক না জানিলেও আলেখ্য কিছুদিন হইতে তাহা সন্দেহ করিতেছিল; এবং হয়ত, এখনই এ লইয়া আলোচনাও করিত না, কিন্তু তিনি নিজেই জিজ্ঞাসা করিলেন—কত টাকা তোমার আবশ্যক বলে মনে হয়, আলো? নিতান্তই যা না হলে নয়, এমনি—
আলেখ্য মনে মনে হিসাব করিয়া কহিল—দাম ঠিক বলতে পারব না বাবা, কিন্তু গোটা-চারেক শোবার ঘর অন্তত: চাই-ই। গোটা-চারেক ড্রেসিং টেবল্, গোটা-দশেক ইজিচেয়ার—
সাহেব সভয়ে বলিয়া উঠিলেন—গোটা-দশেক! একটুখানি থামিয়া অধ্যাপকের প্রতি মুখ তুলিয়া কহিলেন, অমরনাথ, তোমার বিদেশী ছাত্রদের সম্বন্ধে—দেখ, আমি বিশেষ দুঃখিত হয়ে জানাচ্ছি, সাহায্য যে কিছু করে উঠতে পারবো, তা আমার মনে হয় না।
অধ্যাপক শুধু একটু মুচকি হাসিয়া কহিলেন—সে আমারও মনে হয় না, রায়-মশায়।
ক্রোধে আলেখ্যের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। তাহাদের পারিবারিক আলোচনার সূত্রপাতেই যে অপরিচিত অভদ্র লোকটার সরিয়া যাওয়া উচিত ছিল, সে শুধু কেবল বসিয়াই রহিল তাহা নয়, প্রকারান্তরে তাহাতে যোগ দিল, সে-ও আবার বিদ্রূপের ভঙ্গীতে। বিশেষ করিয়া পিতার প্রতি তাহার সম্বোধনের ভাষাটা মেয়ের কানে যেন সূঁচ বিঁধিল। ইহা সত্ত্বেও কিন্তু আলেখ্যের চিরদিনের শিক্ষা তাহাকে অসংযত হইতে দিল না, সে বাহিরের এই ভিক্ষুকটাকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—না হলে হবে কেন বাবা? তা ছাড়া খাটের গদিগুলো সব মেরামত করানো চাই; ঘরে কার্পেট নেই, তাও কিনতে হবে, চা এবং ডিনার সেট সব আনিয়ে দিতে হবে, হয়ত তিন-চার হাজারেও কুলোবে না, আরও বেশী টাকার দরকার হয়ে পড়বে।
বৃদ্ধ দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন—সেইরকমই মনে হচ্ছে বটে।
এত বড় নিশ্বাসের পরে মেয়ের পক্ষে হাসা কঠিন, তবুও সে জোর করিয়াই হাসিয়া বলিল—যে সমাজের যে-রকম রীতি। তাঁরা এলে তুমি ত আর রাইট রয়েল ইন্ডিয়ান স্টাইলে ভাঁড় এবং কলাপাত দিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করতে পারবে না, ইজিচেয়ারের বদলে কুশাসন পেতেও অতিথি-সৎকার চলবে না,—উপায় কি?
রে-সাহেব ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া শেষে আস্তে আস্তে বলিলেন,—বেশ তাই হবে।
বাস্তবিক না হলেই যখন নয়, তখন ভাবনা বৃথা। তা হলে তুমি একটা ফর্দ তৈয়ারি করে ফেল।
আলেখ্য ঘাড় নাড়িয়া কহিল—আমি সমস্ত ঠিক করে নেব বাবা, তুমি কিছু ভেবো না।—একমুহূর্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, তোমার ভাবনার ত কিছুই ছিল না বাবা, শুধু যদি একটুখানি চোখ রাখতে।
পিতা কথা কহিলেন না। বোধ করি, মনে মনে এই কথাই ভাবিতে লাগিলেন যে, দুই চক্ষু ত এখন বিস্ফারিত হইয়াই খুলিয়াছে, কিন্তু দুশ্চিন্তার পরিমাণ তাহাতে কমিতেছে কৈ? মেয়ে কহিল—তোমাকে কিন্তু আমি আর সত্যিই কিছু করতে দেব না বাবা, যা-কিছু করবার, আমিই করব। কত অপব্যয়ই না এই দীর্ঘকাল ধরে নির্বিঘ্নে চলে আসছে। কিসের জন্য এত লোকজন? চোখে দেখতে পায় না, কানে শুনতে পায় না, এমন বোধ হয় বিশ-পঁচিশজন কাছারি জুড়ে বসে আছে। আমরণ তারা কি ফাঁকি দিয়েই কাটাবে? আমি সমস্ত বিদায় দিয়ে ইয়ং মেন বহাল করব। ঠিক অর্ধেক লোকে ডবল কাজ পাব। কতগুলো ঠাকুরবাড়িই রয়েছে বল ত? কত টাকাই না তাতে বৃথা ব্যয় হয়। একা এর থেকেই ত বোধ হয় আমি বছরে দশ-বারো হাজার টাকা বাঁচাতে পারবো।
বৃদ্ধ বোধ করি এতক্ষণ তাঁহার আগচ্ছমান সম্মানিত অতিথিবর্গের কথাই চিন্তা করিতেছিলেন, এদিকে তেমন মন ছিল না, কিন্তু কন্যার শেষ কথাটা কানে যাইবামাত্র একেবারে চমকিয়া উঠিলেন। কহিলেন—কার থেকে বাঁচাবে বলছ মা, দেবসেবা থেকে? কিন্তু সে-সমস্ত যে কর্তাদের আমল থেকে চলে আসছে, তাতে হাত দেবে কি করে?
মেয়ে কহিল—কর্তারা নয় ত কি তোমাকে দোষ দিচ্ছি বাবা, তুমি নিজে কতগুলো পুতুলপূজো বসিয়েছ? অপব্যয়ের সূত্রপাত তাঁরাই করে গেছেন জানি, কিন্তু অন্যায় বা ভুল যাঁরাই কেন না করে থাকুন, তার সংশোধন করা ত প্রয়োজন? তোমার ত মনে আছে বাবা, মা তোমাকে কতদিন এই-সব বন্ধ করে দিতে বলেছেন।
পিতা চুপ করিয়া শুধু একদৃষ্টে কন্যার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সেই বিস্ময়ক্ষুব্ধ চোখের সম্মুখে আলেখ্য কেবলমাত্র যেন নিজের লজ্জা বাঁচাইবার জন্যই সহসা বলিয়া উঠিল—বাবা, তুমি কি এই-সব পুতুলপূজো বিশ্বাস কর?
পিতা কহিলেন, আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের উপর ত এঁদের প্রতিষ্ঠা হয়নি মা !
কন্যা কহিল—তবে তুমি কেন এর ব্যয় বহন করবে, বাবা?
পিতা বলিলেন—আমি ত করিনে, আলো। যাঁরা মাথায় করে এনে স্থাপিত করেছিলেন, আমার সেই পিতৃপিতামহেরাই এখনো তাঁদের ভার বয়ে বেড়াচ্ছেন। যে-সব পুতুল-দেবতাদের তুমি বিশ্বাস করতে পার না মা, তাঁদেরও বঞ্চিত করতে তোমাকে আমি দিতে পারব না।
প্রত্যুত্তরে আলেখ্য পিতার এই হীন দুর্বলতার একটা তীক্ষ্ণ জবাব দিতে যাইতেছিল, কিন্তু একান্ত বিস্ময়ে সে কথা ভুলিয়া গেল। যে অধ্যাপকটি এতক্ষণ নীরবে বসিয়া ছিল, অকস্মাৎ সে হেঁট হইয়া হাত দিয়া সাহেবের বুটের তলা হইতে ধূলা তুলিয়া লইয়া মাথায় দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।
ব্যাপার কি হে, অমরনাথ? তুমি আবার এ কি করলে?
অমর সবিনয়ে কহিল—কিছুই না রায়-মশায়, এসে আপনাকে প্রণাম করা হয়নি, শুধু সেই ত্রুটিটা এখন সেরে নিলাম।
সাহেব বলিলেন—ত্রুটি কিসের হে, আমার মত লোককে তুমি প্রণাম করতে যাবে কিসের জন্যে? আমি ত ব্রাহ্মণই নয় বললে হয়।
অমর কহিল—সে আপনি জানেন, আমি আমার কর্তব্য পালন করলাম মাত্র। অজ্ঞাতে কত ভুল, কত অন্যায়ই না মানুষের হয়।
বুড়া বোধ হয় বুঝিলেন না, বলিলেন—সে ত সর্বদাই হচ্ছে অমরনাথ, মানুষের ভুল-ভ্রান্তির কি আর সীমা আছে? কিন্তু আমাকে প্রণাম না করাটা তোমার ভুলের মধ্যে নয়,—আমি আর ওর যোগ্যই নয়।
অমরনাথ এ কথার প্রতিবাদ করিল না—কোন জবাবই দিল না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।
কিন্তু চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না আলেখ্য। গায়ে পড়িয়া কথা কহা তাহার শিক্ষাও নয়, স্বভাবও নয়, কিন্তু তাহার বিস্ময়ের মাত্রা ক্রোধে পর্যবসিত হইয়া প্রায় অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। কহিল—বাবা, এখন কিন্তু তোমার ওঁর বিদেশী ছাত্রদের সাহায্য না করলেই নয়।
ভালমানুষ বুড়া বিদ্রূপের ধার দিয়াও গেলেন না, আন্তরিক সঙ্কোচের সহিত কহিলেন—সাহায্য করাই ত কর্তব্য মা, কিন্তু তুমি কি মনে কর, এ সময়ে আমরা বিশেষ কিছু করে উঠতে পারবো?
মেয়ে কহিল—সাহায্য যদি কর বাবা, একটু লুকিয়ে ক’রো। তোমার দেব-দ্বিজে ভক্তির কথা রাষ্ট্র হয়ে গেলে বিপদ হবে।
পিতা আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—বিপদ হবে?
অধ্যাপক হাঃ হাঃ হাঃ করিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন—বিপদ হবে না,—আপনি কোন ভয় করবেন না। ড্রেসিং টেব্ল্ আর কাঁটা-চামচে-ডিশের নীচে সমস্ত চাপা পড়ে যাবে।
আঘাত করিতে পাইয়া আলেখ্যের মনের তিক্ততা এই অপরিচিত লোকটির বিরুদ্ধে কতকটা ফিকা হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু অকস্মাৎ অপরের তীক্ষ্ণ পরিহাসের প্রতিঘাতে হঠাৎ সে যেন একেবারে ক্রুর হইয়া উঠিল। আলেখ্য সব ভুলিয়া প্রত্যুত্তরে কহিল, চাপা পড়তে পার বটে, কিন্তু বুটের ধুলোর দামটাও ত আপনাকে দিতে হবে!—কিন্তু বলিয়া ফেলিয়াই সে নিজেই যেন লজ্জায় একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এতবড় নিষ্ঠুর কদর্য কথা যে কি করিয়া তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল, সে ভাবিয়াই পাইল না। রে-সাহেব অত্যন্ত বিস্ময়ে কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি যত সাদাসিধাই হউন, এ কথার তাৎপর্য বুঝিতে পারিলেন। বেহারা আসিয়া স্মরণ করাইয়া দিল যে, ভদ্রলোকগুলি বাহিরের ঘরে বহুক্ষণ অবধি অপেক্ষা করিতেছেন।
বল গে যাচ্ছি, বলিয়া সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন। শান্তকণ্ঠে কহিলেন,—কথাটা তোমার ভাল হয়নি আলো। অমরনাথ, তুমি একটু বসো, আমি এখনি আসছি।—এই বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন। আলেখ্য তাঁহার পিছনে পিছনেই ঘর ছাড়িয়া যাইতে পারিল না। পিতা দৃষ্টির অন্তরালে যাইতেই নিরতিশয় লজ্জার সহিত আস্তে আস্তে কহিল—আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, কিন্তু নিজের ব্যবহারের জন্য আমি অতিশয় দুঃখিত। আমি স্বীকার করছি, আপনাকে ও-কথা বলা আমার ভাল হয়নি।
অধ্যাপক কহিলেন—না, ভাল হয়নি।
এই সোজা কথাটাও আলেখ্যের কিন্তু ভাল লাগিল না। সে এক মুহূর্ত মৌন থাকিয়া কহিল, পিতাকে মর্যাদা দেখালে কন্যার খুশী হবারই কথা। আমার বাবা অত্যন্ত ভালমানুষ, তাঁর সঙ্গে ছলনা কারও আপনার উচিত হয়নি।
অধ্যাপক কহিলেন—ছলনা ত করিনি!
আলেখ্য প্রশ্ন করিল—আড়ম্বর করে হঠাৎ পায়ের ধূলা নেওয়াই কি সত্য?
অধ্যাপক কহিলেন—সত্য বৈ কি।
আলেখ্য বলিল—তা হলে আমার আর কিছুই বলবার নেই। আমি ভুল বুঝেছিলাম।—এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, সহসা দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিল, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে। আপনার পুরোহিতের ব্যবসা, সুতরাং বাবার দুর্বলতায় আপনার উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক, কিন্তু যাঁর ধর্মবিশ্বাস অন্য প্রকারের, ঠাকুর-দেবতা যিনি কোনদিন মানেন না, তাঁর পক্ষে এই অসত্যের প্রশ্রয় দেওয়া কি আপনিই অন্যায় মনে করেন না?
অধ্যাপক মাথা নাড়িয়া কহিলেন—না করিনে। অন্যায় কেবল সেইখানেই হ’ত স্নেহের দুর্বলতায় যদি তিনি আপনাকে প্রশ্রয় দিতেন—তাঁর নিজের অবিশ্বাস যদি তাঁর কর্তব্যকে ডিঙিয়ে যেতো।
অধ্যাপকের জবাবের মধ্যে খোঁচা ছিল। আলেখ্যর দুই ভ্রূ কুঞ্চিত হইল। কহিল—আপনার বক্তব্য এই যে, নিজের বিশ্বাস যার যেমনই হউক, যা চলে আসছে তাকে চলতে দেওয়াই কর্তব্য।
অধ্যাপক হাসিলেন, বলিলেন—আপনার ওটা বিলাতী ঢঙের অত্যন্ত মামুলি যুক্তি। নিজের বিশ্বাসের দাবী একটা আছেই, কিন্তু তার পরের কথা আপনি যখন জানেন না, তখন এ তর্কে শুধু তিক্ততাই বাড়বে, আর কোন ফল হবে না। কিন্তু সে যাক, ঠাকুরবাড়ির পুতুল-দেবতারা সত্যিই হোন, মিথ্যাই হোন, কথা যে কন না, এ কথা খুবই সত্য। তাঁদের অনাহারে রাখলেও তাঁরা আপত্তি করবেন না। কিন্তু এত টাকার বিলাতী আয়না এবং বিলাতী মাটির বাসন কিনলে যারা আপত্তি করবে, তারা কথাও কবে। হয়ত, খুব উঁচু গলাতেই কথা কবে। এ কাজ করবার চেষ্টা আপনি করবেন না।
এইবার তাঁহার সমস্ত কথার মধ্যেই এমন একটা তাচ্ছিল্যের ইঙ্গিত ছিল যে, আলেখ্য নিজেকে শুধু অপমানিত নয়, লাঞ্ছিত জ্ঞান করিল। এতক্ষণ পরে সে যথার্থই ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বারবার এই লোকটিকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার পরিধানের হাতের সূতার মোটা কাপড়, মোটা উত্তরীয় এবং খালি পা লক্ষ্য করিয়া অনুচ্চ কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—আপনি বোধ হয় একজন নন-কো-অপারেটার, না?
অধ্যাপক কহিলেন—হাঁ।
এখানে বটুকদেব কার নাম জানেন?
জানি। আমারই ডাক-নাম।
আলেখ্য কহিল—তাই বটে! তা হলে সমস্তই বুঝেচি। কিন্তু জিনিস কেনা আমার কি করে বন্ধ করবেন? আমার প্রজাদের বোধ করি খাজনা দিতে নিষেধ করে দেবেন?
অধ্যাপক কহিল—অসম্ভব নয়। প্রজাদের অনেক দুঃখের টাকা।
আলেখ্য কহিল—কিন্তু তাতেও যদি বন্ধ না হয়, বোধ হয় ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা করবেন?
অধ্যাপক কহিলেন—ভাঙ্গবো কেন, আপনাকে কিনতেই ত দেব না।
আলেখ্য ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া প্রবল চেষ্টায় ভিতরের দুঃসহ ক্রোধ দমন করিল। শান্তকন্ঠে কহিল— দেখুন, অমরনাথবাবু, এ বিষয়ে আমার শেষ কথাটা আপনি শুনে রাখুন। বাবা নিরীহ মানুষ, কিন্তু আমি নিরীহ নই। তা হলে আমার আসার প্রয়োজন হত না। আপনাদের নন্-কো-অপারেশন ভাল কি মন্দ, আমি জানিনে,—ভালও হতে পারে। কিন্তু আমার প্রজা, আমার আয়-ব্যয়, আমার সাংসারিক ব্যবস্থার সঙ্গে তার ধাক্কা বাধিয়ে দেবেন না। পুলিশকে আমি ভালবাসি নে, তাদের দিয়ে দেশের লোককে শাস্তি দিতে আমার কষ্ট হয়, কিন্তু আমার হাত-পা বেঁধে দিয়ে আমাকে নিরুপায় করে তুলবেন না।—এই বলিয়া সে উত্তরের জন্য অপেক্ষামাত্র না করিয়াই দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছিল, অমরনাথ ডাকিয়া কহিলেন—কিন্তু এমন যদি হয়, আপনি অন্যায় করছেন?
আলেখ্য দ্বারের কাছে থমকিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, আপনার সঙ্গে ন্যায়-অন্যায়ের ধারণা আমার এক না-ও হতে পারে।—এই বলিয়া সে বাহির হইয়া গেল। যে রহিল, সে শুধু অবাক হইয়া সে মুক্ত দ্বারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।
জাগরণ – ০৩
তিন
বিষয়-সম্পত্তির কাজে কন্যার উৎসাহ ও মনোযোগ দেখিয়া রে-সাহেব অত্যন্ত প্রীত হইলেন। ঝাড়া-মোছা হইতে আরম্ভ করিয়া চুন দেওয়া, রং দেওয়া, আসবাবপত্রের পরিবর্তন, পরিবর্জন ইত্যাদিতে সমস্ত বাড়িটারও একদিকে যেমন সংস্কার শুরু হইল, অন্যদিকে শৃঙ্খলাহীন, ঢিলাঢালা জমিদারী সেরেস্তাতেও তেমনিই অত্যন্ত কড়া নিয়ম-কানুনসকল প্রত্যহই জারি হইয়া উঠিতে লাগিল। সাংসারিক সকল ব্যাপারেই অনভিজ্ঞ এই মেয়েটির মধ্যে যে এতখানি কর্মপটুতা ছিল, তাহা পেনশনপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ম্যানেজারবাবু পর্যন্ত স্বীকার না করিয়া পারিলেন না। তাঁহার ত সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবসর নাই। দাখিলা, চিঠা, কবজ, খতিয়ান, রোকড়, রোডসেস্, কাহাকে কি বলে এবং কোথায় কি হয়, জমিদারী কাজের এইসকল পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা লইয়া আলেখ্যের কাছে তিনি ত প্রায় গলদঘর্ম হইয়া উঠিলেন। কর্মচারীদের মধ্যে কাহার কি কাজ, কত বেতন, ফাঁকি না দিলে কতখানি কাজ করা যায়, এ-সকল বুঝিয়া লইতে আলেখ্যের বিলম্ব হইল না। কয়েকটি স্থবির-গোছের লোকের প্রতি প্রথম হইতেই তাহার দৃষ্টি পড়িয়াছিল, জেরার চোটে ম্যানেজার স্বীকার করিয়া ফেলিলেন যে, এইসকল লোকের দ্বারা বস্তুত: কোন উপকারই হয় না, এবং এ কথা তিনি ইতঃপূর্বে সাহেবকে জানাইয়াছিলেন, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। ইনি এই বলিয়া জবাব দিয়াছিলেন যে, এই সংসারে চাকরি করিয়া আজ যাহারা বুড়া হইয়াছে, তাহাদের প্রতি জুলুম করিয়া কাজ আদায় করিবার আবশ্যকতা নাই, নূতন লোক বাহাল করিলেই জমিদারির কাজ চলিয়া যাইবে। এইজন্যই এত লোক বেশী হইয়া পড়িয়াছে।
আলেখ্য কহিল—এবং এইজন্যেই বাবার খরচে কুলোয় না!
ম্যানেজার ব্রজবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।
আলেখ্য কহিল—আমি কাজ চাই, দানছত্র খুলতে চাইনে।
ব্রজবাবু সবিনয়ে কহিলেন, আপনি যেমন আদেশ করবেন, তেমনি হবে।
রে-সাহেব দিন দুই-তিন হইল কলিকাতায় তাঁহার পুরাতন বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন, বাটীতে উপস্থিত ছিলেন না, এই অবকাশে আলেখ্য একদিন ম্যানেজারকে ডাকাইয়া তাঁহার হাতে একখানি ছোট কাগজ দিয়া কহিল—এদের আপনি এই মাসের মাইনেটা চুকিয়া দিয়ে জবাব দিয়ে দেবেন।
বাবা অত্যন্ত দুর্বলপ্রকৃতির মানুষ, তাঁকে জানাবার প্রয়োজন নেই।
ব্রজবাবু কম্পিতহস্তে কাগজখানি গ্রহণ করিলেন; চশমার ভিতর দিয়া নামগুলি একে একে পাঠ করিয়া তাঁহার গলা পর্যন্ত কাঠ হইয়া উঠিল। একটু সামলাইয়া কহিলেন—যে আজ্ঞে। কিন্তু এই নয়ন গাঙ্গুলী লোকটি বড় গরিব, তাঁর—
আলেখ্য কহিল—গরীবের জন্য সংসারে অন্য ব্যবস্থা আছে।
ব্রজবাবু বলিতে গেলেন, তা বটে, কিন্তু—
এ কিন্তুটা আলেখ্য শেষ করিতে দিল না, কহিল—দেখুন ম্যানেজারবাবু, এ নিয়ে আলোচনা স্বভাবতই অপ্রিয়। আমি বিশেষ চিন্তা করেই স্থির করেছি—আপনি এখন যেতে পারেন।
যে আজ্ঞা, বলিয়া বৃদ্ধ ব্রজবাবু কাগজখানি হাতে করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন। শিক্ষিতা জমিদার-কন্যার মেজাজের পরিচয় তিনি পাইয়াছিলেন, তাঁহার আর প্রতিবাদ করিতে সাহস হইল না—পাছে তাঁহার নিজের নামটাও বুড়া ও অকর্মণ্যদের তালিকাভুক্ত হইয়া পড়ে। বিশেষতঃ ইহাও তিনি নিশ্চিত জানিতেন, যাহাদের কাজ গেল, তাহারা কেবল তাঁহার মুখের কথাতেই নিরস্ত হইবে না, আবেদন-নিবেদন সহি-সুপারিশ প্রভৃতি গোলামিগিরির যাহা কিছু দুনিয়ায় প্রচলিত আছে, সমস্তই চেষ্টা করিয়া দেখিবে।
হইলও তাই। পরদিন চারখানা দরখাস্তই ব্রজবাবু আলেখ্যের ঘরে পাঠাইয়া দিলেন। অধীনের নিবেদনে বাঙ্গালাদেশের সেই মামুলি দারিদ্র্যের ইতিহাসও তাহার হেতু। প্রত্যেকেই পরিবারস্থ বিধবাগণের সংখ্যা নির্দেশ করিয়া দিয়াছে, এবং কান্নাকাটি করিয়া জানাইয়াছে যে, সে ভিন্ন তাঁহাদের দাঁড়াইবার আর কোথাও স্থান নাই। আলেখ্য কোনটাই গ্রাহ্য করিল না, এবং প্রত্যেক আবেদনপত্রের নীচেই ইংরাজি প্রথায় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া হুকুম দিল যে, এ বিষয়ে সে সম্পূর্ণ নিরুপায়। ব্রজবাবু ঠিক ইহাই আশা করিয়াছিলেন, তিনি সকলকেই গোপনে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যে, সাহেব ফিরিয়া আসা পর্যন্ত যেন তাহারা ধৈর্য ধরিয়া থাকে। কারণ, চোখের জলের কোন দাম থাকে ত সে কেবল ওই স্বেচ্ছাচারী স্বল্পবুদ্ধি বুড়ার কাছেই আদায় হইতে পারে।
দিন-তিনেক পরে একদিন সকালে আলেখ্য তাহার বসিবার ঘরের বারান্দায় বসিয়া অনেকগুলা নকশার মধ্যে হইতে তাহাদের খাবার ঘরের পেন্টিঙের ডিজাইনটা পছন্দ করিয়া বাহির করিতেছিল।
একজন অতিশয় বৃদ্ধ-গোছের লোক তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। লোকটা যেমন রোগা, তেমনই তাহার পরনের কাপড়-চোপড় ময়লা এবং ছেঁড়া-খোঁড়া।
আলেখ্য মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কে?
লোকটা সহসা জবাব দিতে পারিল না—তোতলা বলিয়া। তাহার পরে কহিল, আমি নয়ন গাঙ্গুলী।
আলেখ্য তাহাকে চিনিতে পারিয়া কঠোরভাবে বলিল—এখানে কেন?
সে কথা বলিবার চেষ্টায় আবার কিছুক্ষণ চোখ ও মুখের নানারূপ ভঙ্গী করিয়া শেষে কহিল—আমার মেয়ের নাম দুর্গা। সে বললে, বাবা তুমি তাঁর কাছে যাও, গেলেই চাকরি হবে। আমার একটি নাতি আছে, তার নাম গণপতি। তার ভারী বুদ্ধি।
ইহার চেহারা দেখিয়াই আলেখ্যের অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল, এই-সকল অসংলগ্ন কথা শুনিয়া বুঝিল, যাহাদের জবাব দেওয়া হইয়াছে, এই লোকটি তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে অপদার্থ। সে নকশার উপর হইতে চোখ না তুলিয়াই কহিল—আমার কাছে কিছু হবে না, আপনি বাইরে যান।
লোকটা তথাপি নড়িল না, সেইখানে দাঁড়াইয়া তাহার সংসারের অবস্থা বর্ণনা করিতে লাগিল। বলিল যে, এই তের টাকা বেতন ভিন্ন তাহাদের আর কিছু নাই। ব্রাহ্মণী জীবিত নাই, বছর-পাঁচেক হইল ছেলেও মারা গিয়াছে, জামাই আসামে চাকরি করিতে গিয়া সন্ন্যাসী হইয়া গিয়াছে, তাহার আর সন্ধান পাওয়া যায় না।
আলেখ্য বিরক্ত হইয়া কহিল—আপনার ঘরের খবর শোনবার আমার ইচ্ছেও নেই, সময়ও নেই; আপনি এখান থেকে যান।
গাঙ্গুলী কর্ণপাতও করিল না, সে কত কি বলিয়া চলিতে লাগিল।
আলেখ্য নিরুপায় হইয়া তখন বেহারাকে ডাকিয়া এই লোকটাকে একপ্রকার জোর করিয়াই বিদায় করিয়া দিয়া পুনরায় নিজের কাজে মন দিল।
কলিকাতা হইতে কিছু কিছু আসবাব আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। পরদিন সকালে একটা মূল্যবান আয়না নিজের শোবার ঘরে খাটাইবার ব্যাপারে আলেখ্য নিজেই তত্ত্বাবধান করিতেছিল, হঠাৎ একটি বছর-দশেকের ছেলের হাত ধরিয়া ম্যানেজার ব্রজবাবু প্রবেশ করিলেন। ছেলেটির পরনের বস্ত্র এত ছেঁড়া যে, নাই বলিলেই হয়। খালি পা, খালি গা, এত কাঁদিয়াছে যে, চোখ দুইটি রক্তবর্ণ হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। আলেখ্য বিস্ময়াপন্ন হইয়া চাহিতে ব্রজবাবু মৃদুকন্ঠে কহিলেন—আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করতে আসতে হ’লো—
কাজের ব্যস্ততার মধ্যে ইহাদের আকস্মিক আগমনে আলেখ্য খুশী হইতে পারে নাই। ঘোষ-সাহেবদের আসার দিন নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে, অথচ বাটী সাজানো-গুছানোর কাজ এখনও বিস্তর বাকি; কহিল—নিতান্ত জরুরী কাজ নাকি?
ব্রজবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, নয়ন গাঙ্গুলীর কামাইয়ের দরুন পাঁচ টাকা মাইনে কাটা হয়েছিল, কিন্তু পরে বিবেচনা করবেন বলে একটা ভরসা দিয়েছিলেন—
আলেখ্য অপ্রসন্নমুখে বলিল—সে বিবেচনার আমি আর প্রয়োজন দেখিনে।
ব্রজবাবু প্রতিবাদ করিতে বোধ হয় সাহস করিলেন না, ছেলেটিকে লইয়া নিঃশব্দে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, আলেখ্য কৌতূহলবশে সহসা জিজ্ঞাসা করিল—ছেলেটি কে ম্যানেজারবাবু, তাঁর নাতি বোধ করি?
ছেলেটি নিজেই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—হ্যাঁ, এবং বলিয়াই কাঁদিয়া ফেলিল। ব্রজবাবু তখন আস্তে আস্তে কহিলেন, চাকরি নেই শুনে মুদী কাল আর চাল-ডাল কিছু দিলে না, হয়ত তার বাকীও ছিল—সারাদিন খাওয়া-দাওয়া কারও হ’ল না। ছেলে-জামাইয়ের শোকে বুড়ো বয়সে ইদানীং গাঙ্গুলী মশায়ের মাথাটাও তেমন ভাল ছিল না,—কি ভাবলে কি জানি, রাত্রেই কতকগুলো কলকে ফুলের বীচি বেটে খেয়ে আত্মহত্যা করে ফেলে—এখন আবার পুলিশ না এলে দাহ পর্যন্ত হওয়া—
আলেখ্য চমকাইয়া উঠিয়া কহিল—কে আত্মহত্যা করলে?
ছেলেটি কাঁদিতেছিল, বলিল—দাদামশাই।
দাদামশাই? নয়ন গাঙ্গুলী? আত্মহত্যা করেছেন?
ব্রজবাবু বলিলেন—হাঁ, ভোরবেলায় মারা গেছেন। টাকা পাঁচটা পেলে, এদের বড় উপকার হয়। ছেলেটিকে কহিলেন—মণি, হাতজোড় করে বল, মা, আমাদের পাঁচ টাকা ভিক্ষে দিন। বল!
ছেলেটি কাঁদিতে কাঁদিতে হাতজোড় করিয়া তাঁহার কথাগুলা আবৃত্তি করিল। আর তাহার প্রতি অনিমেষ-চক্ষে চাহিয়া আলেখ্য মূর্তির মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।
মণিকে লইয়া ব্রজবাবু চলিয়া গেলেন। নয়ন গাঙ্গুলীর মৃতদেহের প্রায়শ্চিত্ত হইতে শুরু করিয়া সৎকার পর্যন্ত কিছুই টাকার অভাবে আর আটকাইয়া থাকিবে না, যাবার সময় তাহা তিনি বুঝিয়া গেলেন; কিন্তু আলেখ্যের কাছে ঘরের পেন্টিং হইতে সাজানো-গোছানো যা-কিছু কাজ সমস্তই একেবারে অর্থহীন হইয়া গেল। সেখান হইতে বাহির হইয়া সে তাহার বসিবার ঘরে আসিয়া চুপ করিয়া বসিল।
মিস্ত্রী আসিয়া আলমারি রাখিবার জায়গা দেখাইয়া দিতে কহিলে আলেখ্য বলিল—এখন থাক।
সরকার আসিয়া খাবার কথা জিজ্ঞাসা করিলে কহিল—যা হয় হোক, আমি জানিনে।
একটা মেরামতির কাজের হুকুম লইতে আসিয়া ঠিকাদার ধমক খাইয়া ফিরিয়া গেল। আলেখ্যের কেবলই মনে হইতে লাগিল, কিছুতেই আর তাহার প্রয়োজন নাই, এদেশে আর সে মুখ দেখাইতে পারিবে না। নবীন উদ্যমে বিলাতী প্রথায়, কড়া নিয়মে কাজ করিতে গিয়া আরম্ভেই সে যে এতবড় ধাক্কা খাইবে, তা কল্পনাও করে নাই। এ কি হইয়া গেল? বিদ্বেষবশে কাহারও প্রতি সে কোন অন্যায় করে নাই—হয়ত একটা ভুল হইয়াছে, কিন্তু এত বড় শাস্তি? একেবারে সে আত্মহত্যা করিয়া তাহার প্রতিশোধ দিল!
একজন ছোট-গোছের কর্মচারীকে গোপনে ডাকাইয়া আনিয়া সে একটি একটি করিয়া সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিল। নয়ন গাঙ্গুলী এই সংসারে চল্লিশ বৎসর একাদিক্রমে চাকরি করিয়াছে; বাস্তবিকই সে অত্যন্ত দরিদ্র, খান-দুই মাটির ঘর ছাড়া আর তাহার আপনার বলিত এত বড় পৃথিবীতে কোথাও কিছু ছিল না,—এই তেরটি টাকা বেতনের উপরই তাহাদের সমস্ত নির্ভর, ইহার কিছুই মিথ্যা নয়।
তেরটি টাকা কি-ই বা! অথচ একটা দরিদ্র পরিবারের সমস্ত খাওয়া-পরা, সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-নিরানন্দ, মাসের পর মাস বছরের পর বছর ইহাকে আশ্রয় করিয়াই জীবনধারণ করিয়াছিল।
এই টাকা কয়টি কত তুচ্ছ। তাহার অসংখ্য জোড়া জুতার মধ্যে এক জোড়ার দামও ইহাতে কুলায় না। কিন্তু আজ একটা লোক নিজের জীবন দিয়া যখন ইহার সত্যকার মূল্য তাহার চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিল, তখন বুকের ভিতর যেন ঝড় বহিতে লাগিল। ঐ সারাদিনের উপবাসী ছেলেটার ফুলিয়া ফুলিয়া কান্নার শব্দ তাহার কানের মধ্য দিয়া কোথায় কি করিয়া যে বিঁধিয়া ফিরিতে লাগিল, সে তাহার কূল-কিনারা খুঁজিয়া পাইল না।
সেইখানে চুপ করিয়া বসিয়া আলেখ্যের কত দিনের কত অর্থ-ব্যয়ের কথাই না মনে পড়িতে লাগিল। তাহার নিজের, তাহার স্বর্গগত জননীর, তাহার পরিচিত বন্ধুবান্ধবের, তাহাদের সভ্য-সমাজের কতদিনের কত উৎসব, কত আহার-বিহার, গান-বাজনার আয়োজন, কত বস্ত্র, কত অলঙ্কার, কত গাড়ি-ঘোড়া, ফুল-ফল, কত আলোর মিথ্যা আড়ম্বর,—তাহার পরিমাণ কল্পনা করিয়া তাহার শিরার রক্ত শীতল হইয়া আসিতে চাহিল।
হাতের কাছে ছোট টিপয়ের উপরে নূতন আয়নার বিলটা পড়িয়া ছিল, তাহার অঙ্কের প্রতি চোখ পড়িতেই আজ তাহার প্রথম মনে হইল, এই বস্তুটায় তাহার কতটুকুই বা প্রয়োজন, অথচ ইহারই মূল্যে একজন লোক অনায়াসে পাঁচ বৎসরকাল বাঁচিতে পারিত! আজ তাহার নিজের হাতে প্রাণ বাহির করিবার আবশ্যক হইত না!
আজ বিকালের গাড়িতে রে-সাহেবের বাড়ি আসিবার কথা। পিতার দুর্বলতার প্রতি তাহার অতিশয় অশ্রদ্ধা ছিল, ইহা সে মায়ের কাছে শিখিয়াছিল। পরের অন্যায়কে তিনি জোর করিয়া খণ্ডন করিতে পারেন না, তাঁহার চক্ষুলজ্জায় বাধে। এই দৌর্বল্যের সুযোগ লইয়া কত লোক তাঁহার প্রতি অসঙ্গত উৎপাত করিয়া আসিয়াছে, তিনি কোনদিন কোন কথা বলিতে পারেন নাই। এই-সকল পীড়নের শেষ করিয়া দিতে আলেখ্য বদ্ধপরিকর হইয়া লাগিয়াছিল। প্রাচীন, অলস ও অকেজো লোকগুলাকে বিদায় দিবার প্রস্তাবে সামান্য একটুখানি প্রতিবাদ করিয়া যখন ব্রজবাবু পূর্বের কথা তুলিয়া বলিয়াছিলেন,—সাহেবের ইহাতে সম্মতি নাই, আলেখ্য তখন সে কথায় কর্ণপাত করে নাই। পিতার চিরদিনের দুর্বলতা স্মরণ করিয়াই সে তাঁহার অবর্তমানেই এ সমস্যার মীমাংসা করিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু আজ অক্ষম অতিবৃদ্ধ নয়ন গাঙ্গুলী যখন তাহার স্বহস্তের মৃত্যু দিয়া সংসারের একটা অপরিজ্ঞাত দিকের পর্দা তুলিয়া ফেলিল, তখন সেইদিকে চাহিয়া এই অনভিজ্ঞ মেয়েটির গভীর পরিতাপের সহিত একলা বসিয়া অনেক নূতন প্রশ্নের সমাধান করিবার আবার প্রয়োজন হইয়া পড়িল। অনুপস্থিত শক্তিহীন পিতাকে স্মরণ করিয়া সে বারবার বলিতে লাগিল, চিত্তের কোমলতা এবং দুর্বলতা এক বস্তু নয় বাবা, তোমাকে আমরা চিরদিন ভুল বুঝিয়াছি, কিন্তু কোনদিন তুমি অভিযোগ কর নাই। সেই পিতাকে মনে করিয়াই আজ সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, সংসার শুধুই একটা মস্ত দোকান-ঘর নয়। কেবল জিনিস ওজন করিয়া মূল্য ধার্য করিলেই মানুষের সকল কার্য সমাপ্ত হয় না। এখানে অক্ষমেরও বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার আছে,—তাহার কাজ করিবার শক্তি লোপ পাইয়াছে বলিয়া তাহার জীবনধারণের দাবীও বিলুপ্ত করা যায় না।
আগে সকালে বিকালে কাছারি বসিত, আলেখ্য অন্যান্য অফিসের নিয়মে তাহাকে ১১টা হইতে ৪টায় দাঁড় করাইয়াছিল।
এই সময়ের অনেকখানি সময় সে নিজে গিয়া ম্যানেজারের ঘরে বসিয়া কাজকর্ম দেখিত, আজ কিন্তু সে নিজের কর্মচারীদের কাছে মুখ দেখাইতে পারিল না, আপনাকে সেইখানেই আবদ্ধ করিয়া রাখিল। খাওয়া-দাওয়া তাহার ভাল লাগিল না এবং এমনই করিয়া যখন সারাবেলা কাটিল, তখন বৈকালের দিকে জানালা দিয়া দেখিতে পাইল, সাহেবের খালি গাড়ি স্টেশন হইতে ফিরিয়া আসিল, তিনি আসেন নাই। কোথাও আসা-যাওয়া সম্বন্ধে তাঁহার কথার কখনও ব্যতিক্রম হইত না; এই দিক দিয়া সে পিতার জন্য যেমন চিন্তা বোধ করিল, তাঁহার না আসায় আর একদিকে তেমনই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। তিনি রাগ করিবেন না, একটি কঠোর বাক্য পর্যন্তও হয়ত উচ্চারণ করিবেন না, ইহা সে নিশ্চয় জানিত; কিন্তু তাঁহার ব্যথিত নিঃশব্দ প্রশ্নের সে যে কি জবাব দিবে, কোনমতেই খুঁজিয়া পাইতেছিল না। সেই কঠিন দায় হইতে সে আজিকার মত অব্যাহতি লাভ করিয়া যেন বাঁচিয়া গেল। এই শান্তিটুকু তখনও সে নিজের মধ্যে অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছিল, বেহারা আসিয়া সংবাদ দিল, ঠাকুরমশাই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।
কে ঠাকুরমশাই? কোথায় তিনি?
ঠিক পর্দার আড়াল হইতে উত্তর আসিল—আমি অমরনাথ, এই বাইরেই দাঁড়িয়ে আছি।
‘আসুন’ বলিয়া আহ্বান করিয়া আলেখ্য উঠিয়া দাঁড়াইল। প্রত্যাখ্যান করিবার সময় বা সুযোগ তাহার রহিল না।
আলেখ্য হাত তুলিয়া নমস্কার করিল, কিন্তু সেদিনের মত আজও অধ্যাপক সোজা দাঁড়াইয়া রহিলেন, নমস্কার ফিরাইয়া দিবার চেষ্টামাত্রও করিলেন না। আলেখ্য লক্ষ্য করিল, কিন্তু কাহারও কোনপ্রকার আচরণেই ত্রুটি ধরিবার মত মনের জোর আজ তাহার ছিল না।
অধ্যাপক নিজেই আসন গ্রহণ করিলেন। কহিলেন, অত্যন্ত বিশেষ প্রয়োজনেই আপনার কাছে আজ আমাকে আসতে হয়েছে, না হলে আসতাম না।
এই মানুষটি গ্রামের সকল কাজেই আছেন, অতএব তিনি যে নয়ন গাঙ্গুলীর ব্যাপারেই আসিয়াছেন, আলেখ্য মনে মনে তাহা বুঝিল, এবং পিতার অবর্তমানে তাঁহাকে কি জবাব দিবে, চক্ষুর নিমেষে স্থির করিয়া লইয়া শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—বলুন।
অধ্যাপক একটুখানি হাসিলেন; বলিলেন—আজ আপনি নিজের মধ্যে যে কত দুঃখ পেয়েছেন, সে আর কেউ না জানলেও আমি জানি। সে আলোচনা করতে আমি আসিনি, আমি আপনার শত্রু নই।
আলেখ্যর বোধ হইল, এই লোকটি যেন তাহাকে বিদ্রূপ করিতে আসিয়াছে, কিন্তু নিজেকে সে চঞ্চল হইতে দিল না, তেমনই সহজভাবেই কহিল—আপনার প্রয়োজন বলুন।
অধ্যাপক কহিলেন—বলছি। কাল হাটের দিন, শহর থেকে পুলিশ এসে এর মধ্যেই সমস্ত ঘিরে ফেলেছে। এ কাজ আপনি কেন করতে গেলেন?
আলেখ্য চমকিত হইল। এখানে আসার পরদিনই সে বিশেষ কোন অনুসন্ধান বা চিন্তা না করিয়াই জিলার ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট একখানা চিঠি পাঠাইয়া দিয়াছিল। হাটের সম্বন্ধে যে-সকল কথা সে লিখিয়াছিল, তাহার অধিকাংশই অতিরঞ্জিত বা সত্য-মিথ্যায় বিজড়িত। ইহার ফলাফল সে ঠিক জানিত না এবং বিলম্ব দেখিয়া ভাবিয়াছিল হয়ত সে চিঠি পৌঁছায় নাই, কিংবা পৌঁছাইলেও ম্যাজিস্ট্রেট ইহার কিছুই করিবেন না। এতদিনের ব্যবধানে চিঠির কথা সে নিজেই প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল, অকস্মাৎ আজ এই খবর।
আলেখ্য নরম হইয়া বলিল—বেশ ত, এলেই বা তারা, কি এমন ক্ষতি?
অধ্যাপক কহিলেন—আপনি বিদেশে ছিলেন, জানেন না, কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, সহজে এর শেষ হবে না—দু’চারজন মারাও যদি যায় ত আমি আশ্চর্য হব না।
আলেখ্য ভীত হইয়া বলিল—মারা যাবে? কে মারা যাবে?
অধ্যাপক কহিলেন—কে মারা যাবে, কি বলবো? হয়ত আমিও যেতে পারি।
আপনি?
বিচিত্র কি? আত্মসম্মানের জন্যে যদি মরবার প্রয়োজনই হয়, আমাকেই ত সকলের আগে যেতে হবে। কিন্তু সব কথা আপনাকে বলবার এখন আমার সময় নেই, আমাকে অনেকদূরে যেতে হবে। কাল সকালে কি একবার দেখা হতে পারে?
আলেখ্য ব্যগ্র হইয়া বলিল—পারে। আপনি যখনই আমাকে ডেকে পাঠাবেন, আমি তখনই এসে হাজির হব। বাবা নেই, আমাকে কিন্তু আপনি মিথ্যে ভয় দেখাবেন না।
তাহার ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে আক্রমণের লেশমাত্রও ছিল না, অধ্যাপক শুধু একটুখানি হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—না, ভয় দেখানো আমার অভ্যাস নয়, কিন্তু কাল যেন সত্যই আপনার দেখা পাই।—এই বলিয়া যেমন সহজে আসিয়াছিলেন, তেমনই সহজে বাহির হইয়া গেলেন। (‘মাসিক বসুমতী,’ পৌষ ১৩৩০।
জাগরণ – ০৪
চার
সন্ধ্যা সবেমাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু চাকররা তখন পর্যন্ত ঘরে আলো দিয়া যায় নাই। শ্রান্তি, পরিতাপ ও দুশ্চিন্তার গুরুভারে আলেখ্য সেইখানেই চুপ করিয়া বসিয়া ছিল, উপরে নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িবার জোরটুকুও যেন তাহাতে ছিল না, এমন সময়ে একজন অতিশয় বৃদ্ধগোছের ভদ্রলোক বলা নাই, কওয়া নাই, দ্বারের পর্দা সরাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন। আলেখ্য বিস্মিত ও বিরক্তচিত্তে সোজা হইয়া বসিয়া কহিল—কে?
বৃদ্ধটি সম্মুখের একখানি চেয়ার সযত্নে ও সাবধানে টানিয়া লইয়া বসিতে বসিতে কহিলেন—আমার নাম নিমাই ভট্টাচার্য, দূরসম্পর্কে অমরনাথের আমি ঠাকুরদাদা হই,—আর শুধু অমরনাথের বলি কেন, এ অঞ্চলে সকলেরই আমি ঠাকুর্দা, আমার চেয়ে বুড়ো আর এদিকে কেউ নেই। তোমার বাবা রাধামাধবও ছেলেবেলায় আমাকে খুড়ো বলে ডাকতেন। কাশীতে ছিলাম, হঠাৎ যে গরম পড়েছে, টিকতে পারলাম না। যে যাই বলুক দিদি, বাঙ্গালাদেশের মত দেশ আর নেই—যেন স্বর্গ। এখানে এসে কেমন আছ? বাবা ভাল আছেন?
আলেখ্য ঘাড় নাড়িয়া কহিল—হাঁ, তিনি ভাল আছেন। আপনার কি প্রয়োজন? বাবা কিন্তু আজ বাড়ি নেই।
নিমাই বলিলেন—কিন্তু তাঁর ত আজ ফেরবার কথা ছিল?
আলেখ্য কহিল—ছিল, কিন্তু যে কারণেই হোক ফিরতে পারেন নি। কাল তিনি এলে আপনি দেখা করবেন।
বৃদ্ধ আলেখ্যের মুখের প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—না দিদি, আমার বেশ সচ্ছল অবস্থা, আমি ভিক্ষের জন্যে আসিনি। অমরনাথের মুখে শুনেছি, তুমি নাকি বিলেত পর্যন্ত গেছ। ভাল লেখাপড়া-জানা মেয়েদের আমি বড় ভালবাসি। তাদের সঙ্গে দুটো কথা কইবার আমার ভারী লোভ, কিন্তু কখনও সে সুযোগ পাইনি। তারা আমার মত একজন নগণ্য বুড়োমানুষের সঙ্গে কথা কইতে চাইবেই বা কেন? তাই ভাবলাম, ঘরের কাছে যদি এতবড় সুবিধে পাওয়াই গেছে ত ছাড়া হবে না। ক’টা দিনই বা বাঁচবো, কিন্তু বুড়োর উপর তুমি ত মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠছ, না দিদি?
আলেখ্য মনে মনে লজ্জা পাইয়া সবিনয়ে কহিল—আজ্ঞে না; শুধু আজ বড় ক্লান্ত ছিলাম বলেই নিমাই বলিলেন সে আমি শুনেছি দিদি, অমরনাথ আমার কাছে সমস্ত বলেই তবে গেছেন। বড় ভাল ছেলে, এতখানি বয়সে তার আর জোড়া কোথাও দেখলাম না। পাগলা দুঃখের জ্বালা সইতে পারলে না, আপনাকে হত্যা করে ফেললে,—আহা! তাই ভাবি, দিদি, ভগবান শক্তি হরণ করে নিলে মানুষ কি-ই বা! আসবার পথে তাদের বাড়ির পাশ দিয়েই আসছিলাম, শ্মশান থেকে এখনও তারা ফেরেনি, ভেতরে মেয়েটা ডাক ছেড়ে চেঁচাচ্ছে,—আহা! সংসারে লঘু পাপে কত গুরু দণ্ডই না হয়! জিনিস হয়ে বয়ে চুকে যায়, কিন্তু দাগ তার সারা জীবনে মিলোয় না। ভাবলাম, একবার ভেতরে ঢুকে গিয়ে বলি, দুর্গা, অভিসম্পাত করে আর লাভ কি মা, সে যদি জানত, এতবড় ভয়ানক কাণ্ড হবে, তা হলে কি কখনও তোমার বাবাকে জবাব দিতে পারতো? তাকে আমি চিনিনে, তবু বলছি কখ্খনো না। যা হবার তা হয়েছে, কিন্তু যে বেঁচে রইল, তার মনস্তাপ কি কখনও ঘুচবে! এ কলঙ্কের দাগে তাকে চিরকাল দাগী হয়ে থাকতে হবে। অথচ তলিয়ে দেখলে এ ত সত্য নয়। তোমার মুখ দেখেই আমি বুঝতে পারছি দিদি, তার মেয়ের চেয়ে এ দুর্ঘটনা তোমাকে ত কম আঘাত করেনি!
এই আগন্তুকের অবাঞ্ছিত আগমনে আলেখ্যের পীড়িত চিত্ত তিক্ততায় পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার মন্তব্য শেষ হইলে সে সবিস্ময়ে ক্ষণকাল তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিল—আপনাকে কে বললে আমি আঘাত পেয়েছি?
বৃদ্ধ কহিলেন—অমরনাথ আমাকে ত তাই বলে গেলেন।
আলেখ্য তেমনিই আস্তে আস্তে বলিল—অমরনাথবাবুর এরূপ অনুমানের হেতু কি, তা তিনিই জানেন। গাঙ্গুলীমশাই সম্পূর্ণ কাজের বার হয়ে গিয়েছিলেন। আমার জমিদারি সুশৃঙ্খলায় চালাবার চেষ্টা করা ত আমার অপরাধ নয়।
নিমাই বলিলেন—তোমার অপরাধের উল্লেখ ত সে একবারও করেনি দিদি।
আলেখ্য প্রত্যুত্তরে শুধু কহিল—আমি আমার কর্তব্য করেছিলাম মাত্র।
তাহার জবাব শুনিয়া বৃদ্ধ অন্ধকারে ঠাহর করিয়া তাহার মুখের চেহারা লক্ষ্য করিবার চেষ্টা করিয়া শেষে একটুখানি হাসিলেন।
বলিলেন—কর্তব্যের কি বাঁধাধরা কোন হিসেব আছে ভাই, যে, এই শক্ত সোজা জবাবটা দিয়েই এ সত্তর বছরের বুড়োটাকে ঠকিয়ে দেবে? বুদ্ধিহত অক্ষম এই যে দুঃখী মানুষটা তোমার অন্নেই চিরদিন প্রতিপালিত হয়ে অবশেষে তোমার ভয়েই কূল-কিনারা না পেয়ে নিজের প্রাণটাকে হত্যা করে সংসার থেকে বিদায় নিলে, কর্তব্যের দোহাই দিয়ে কি এর দুঃখকে ঠেকানো যায় দিদি? নিরুপায় মেয়েটা তার শোকে চেঁচাচ্ছে, তার উপবাসী নাতিটা গেছে কাঁদতে কাঁদতে শ্মশানে—এর দুঃখের কি আদি-অন্ত আছে? আমি যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি দিদি, একলা ঘরের মধ্যে বসে ব্যথায় তোমার বুক ফেটে যাচ্ছে।—এই বলিয়া বৃদ্ধ উত্তরীয়-প্রান্তে নিজের দুটি আর্দ্র চক্ষু মার্জনা করিতে গিয়া সহসা সম্মুখে শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন। এতক্ষণ আলেখ্য কোনমতে সহিয়াছিল, কিন্তু কথা তাঁহার সম্পূর্ণ শেষ না হইতেই সুমুখের টেব্লে সজোরে মাথা রাখিয়া একেবারে হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।
বুড়া নিমাই নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। অসময়ে সান্ত্বনা দিয়া তাহার কান্না থামাইবার চেষ্টামাত্র করিলেন না। মিনিট পাঁচ-ছয় এইভাবে কাটিলে আলেখ্য উঠিয়া বসিয়া নিজের চোখ মুছিতে লাগিল।
এতক্ষণে নিমাই কথা কহিলেন। সস্নেহ মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন—এ আমি জানতাম দিদি। এ নইলে কিসের শিক্ষা, কিসের লেখাপড়া! এতবড় জমিদারির বোঝা সাধ্য কি তোমার বইতে পার!
কোন কারণে কাহারও কাছেই বোধ করি এমন করিয়া আলেখ্য আপনার দুর্বলতা প্রকাশ করিতে পারিত না, কিন্তু আজ সে এই অপরিচিতের কাছে নিজে মর্যাদা বাঁচাইবার এতটুকু চেষ্টা করিল না। হয়ত সে শক্তিও তাহার ছিল না। অশ্রুরুদ্ধ ভগ্নস্বরে সহসা বলিয়া উঠিল—আপনাদের দেশে এসেছিলাম আমি থাকতে, কিন্তু এর পরে এখানে মুখ দেখাতেও পারব না।
বৃদ্ধ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—এ লজ্জা যে তোমার মিথ্যে, এ মিথ্যে সান্ত্বনা তোমাকে আমি দেব না। কিন্তু সমস্ত যদি চিরকালের মত ত্যাগ করে যেতে পারো, তবেই এ যাওয়ার অর্থ হবে, নইলে যতদূরেই কেন যাও না, এই রস শোষণ করেই যদি তোমাকে জীবনধারণ করতে হয় ত আর একজনের জীবন-হরণের পাপ থেকে তুমি কোনদিন মুক্তি পাবে না। এখানকার লজ্জা সেখানে চাপা দিয়েই যদি মুখ দেখাতে হয় দিদি, আমি বলি, তা হলে লোক ঠকিয়ে আর কাজ নেই। তুমি এখানেই থাকো।
আলেখ্য বলিল—কিন্তু আমি যে সত্যিকার অপরাধ কিছু করিনি, এখানকার লোকে ত তা বুঝতে চাইবে না।
নিমাই কহিলেন—বুঝতে চাওয়া ত উচিতও নয়।
আলেখ্য সহসা একটু কঠিন হইয়া বলিল—এ কথা আমি কোনমতেই স্বীকার করতে পারিনে।
বৃদ্ধ তৎক্ষণাৎ তাহার মুখের উপরেই জবাব দিলেন—আজ হয়ত পার না, কিন্তু আমি তোমাকে আশীর্বাদ করি, আর একদিন যেন এ সত্য সবিনয়ে স্বীকার করার মত সাহস তোমার হয়।
ভৃত্য বাতি দিয়া গেল। সেই আলোকের সম্মুখে আলেখ্য কিছুতেই মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না। নিমাই কহিতে লাগিলেন—তুমি শিক্ষিতা মেয়ে, অনেক দূর থেকে তোমাকে আমি দেখতে এসেছি। যে শিক্ষা তুমি পেয়েছ, হয়ত সে কেবল এই কথাই তোমাকে শিখাতে চেয়েছে যে, এ দুনিয়ায় যোগ্যতাটাই একমাত্র এবং অদ্বিতীয়। কিন্তু আমাদের এই সোনার দেশ কোনদিন কিছুতে এ কথা স্বীকার করেনি। এদেশে অক্ষম, দুর্বল, একান্ত অযোগ্যেরও দুটো ভাত-কাপড়ের দাবী আছে। অযোগ্যতার অপরাধে বাঁচার অধিকার থেকে সংসারে কেউ তাকে বঞ্চিত করতে পারে না; কিন্তু গাঙ্গুলীকে তাই তুমি করলে। তাদের সকল দুঃখের ইতিহাস শুনেও তোমার খাতা লেখবার যোগ্যতা দিয়েই শুধু তার প্রাণের মূল্য ধার্য করে দিলে। তুমি স্থির করলে, যে তোমার খাতা লিখতে আর পারে না, তার খাওয়া-পরার ওই ক’টা টাকা খরচ না হয়ে তোমার সিন্দুকে জমা হওয়াই দরকার। এই না দিদি?
আলেখ্যর কণ্ঠস্বর পুনরায় রুদ্ধ হইয়া আসিল, কহিল—আমি কখ্খনো এত কথা ভেবে করিনি। আমি কিছুতেই এত হীন নই।
নিমাই বলিলেন—সে আমি জানি, তাই ত তোমার শিক্ষার কথা আমি বলছিলাম দিদি। অমরনাথ বলছিলেন, তোমার জামা-কাপড়-জুতো-মোজার খরচ,—তিনি বলছিলেন, তোমার আয়না-চিরুনি-সাবান-গন্ধের অত্যন্ত ব্যয়; একজনের ভাত-কাপড়ের প্রয়োজনের চেয়ে আর একজনের এইগুলোর প্রয়োজন যে কোন অবস্থাতেই বড় হতে পারে, এ কুশিক্ষা যদি কোথাও পেয়ে থাক ত সে তোমাকে আজ ভুলতে হবে। যারা জন্মেছে, তারা যত দুর্বল, যত অক্ষম, যত পীড়িতই হোক, বাঁচবার অধিকারে তাদের কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারে না, এ সত্য তোমাকে শিখতেই হবে।
এত বড় জমিদারির দৈবাৎ আজ তুমি মালিক, তাই তোমার বিলাসিতার উপকরণ যোগাতে আর একজনকে অনাহারে আত্মহত্যা করতে হবে, এ ত হতেই পারে না; এবং যে সমাজবিধানে এত বড় অন্যায় করাও তোমার পক্ষে আজ সহজ হতে পারলে, এ বিধান যতদিনেরই প্রাচীন হোক, কিছুতেই এটা মানুষের সমাজের চূড়ান্ত এবং শেষ বিধান হতে পারে না। আমি বুড়ো হয়েছি, সেদিন চোখে দেখে যাবার আমার সময় হবে না, কিন্তু এ কথা তুমি নিশ্চয় জেনো দিদি, অক্ষম অকর্মণ্য বলে আজ যাদের তোমরা বিচারের ভান করছ, তাদেরই ছেলেপুলেদের কাছে আর একদিন তোমাদেরই কর্মপটুতার জবাবদিহি করতে হবে। সেদিন মনুষ্যত্বের আদালতে কেবল জমিদারির মালিক বলেই আরজি পেশ করা চলবে না।
আলেখ্য তাঁহার কথাগুলি যে বিশ্বাস করিল, তাহা নয়। বরঞ্চ, আর কোন সময়ে এই সকল অপ্রিয় কঠিন আলোচনায় সে মনে মনে ভারী রাগ করিত। কিন্তু আজিকার দিনে কতক কৌতুহলবশে, কতক বা লজ্জায় ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল—প্রজারা কি বিদ্রোহ করবে আপনি বলছেন? তাদের কি সব এইরকম মনের ভাব?
নিমাই কহিলেন—দিদি, বিদ্রোহ শব্দটা শুনতে খারাপ, অনেকেই ওটা পছন্দ করে না; এবং মনোভাব জিনিসটা অত্যন্ত অস্থির বস্তু। ওর নিজের কোন ঠাঁই নেই, অর্থাৎ ওটা নিছক অবস্থা এবং শিক্ষার ফল। এরা কাঁধ মিলিয়ে দ্রুতবেগে যেদিকে চলেছে, আমি শুধু তার দিকেই তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এদের ঠেকাতে না পারলে ওকেও ঠেকাতে পারা যাবে না। জগতে বুদ্ধিমানরা এতকাল তাদের আফিং খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল, আজ হঠাৎ তাদের ক্ষিদের জ্বালায় ঘুম ভেঙ্গে গেছে। পেট না ভরলে আর যে তারা নীতির বচন এবং পুরানো আইন-কানুনের চোখ-রাঙানিতে থামবে এমন ত ভরসা হয় না দিদি।
আলেখ্য কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কি বলেন এ-সমস্তই তবে বিলাতী শিক্ষার দোষ?
বৃদ্ধ কহিলেন—আমি দোষের কথা ত একবারও বলিনি দিদি। আমি বলি, এ তার ফল।
আলেখ্য কহিল—কুফল।
বৃদ্ধ হাসিলেন। বলিলেন—কথাটা একটু গুলিয়ে গেল ভাই। তা যাক। আমি সুফল-কুফলের উল্লেখ করিনি, শুধু ফলের কথাই বলেছিলাম।
ভাল, সেই কথাই যদি উঠলো, তবে বলি দিদি, আমার জীবনেই আমি দেখেছি, ছ’টা পয়সা ও এক পাতা দোক্তার বদলে একটা লোক সারাদিন মজুরি করে তার পরিবার প্রতিপালন করেছে। দুঃখে নয়, সচ্ছলে—আনন্দের সঙ্গে। দেশে টাকা ছিল না, কিন্তু প্রচুর খাদ্য ছিল। রেল ছিল না, জাহাজ ছিল না—বিদেশী সাহেব আর ততোধিক বিদেশী মারবাড়ীতে মিলে দেশের অন্ন বিদেশে চালান দিয়ে তখন সহস্র কোটি লোকের জীবন-সমস্যা এমন দুঃসহ, এমন ভীষণ জটিল করে তোলবার সুযোগ পেত না। তখন ক্ষুধাতুরের মুখের গ্রাস জুয়ার আড্ডার মধ্যে দিয়ে এমন করে সোনা-রূপোয় রূপান্তরিত হয়ে যোগ্যতমের সিন্দুকে গিয়ে উপস্থিত হ’ত না।—বলিতে বলিতে হঠাৎ বৃদ্ধের দুই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল, কহিলেন—দিদি, আমার ছেলেবেলায় অক্ষম অযোগ্যের বেঁচে থাকবার অধিকার নিয়ে এমন নিষ্ঠুর পরীক্ষা ছিল না। আজ একমুঠো শাকান্নও দেশে নষ্ট হবার নয়, বুদ্ধিমান ও ব্যবসায়ীতে মিলে তাঁবার টুকরোয় তাকে দাঁড় করাতে দেরি করে না—অর্থবিজ্ঞানের পণ্ডিতরা বলবেন, এর চেয়ে মঙ্গল আর কি আছে। কিন্তু আমার মত যাকে গ্রামে গ্রামে দুঃখীদের মাঝখানে ঘুরে বেড়াতে হয়, সেই জানে মঙ্গল এতে কত!
এই বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর ও মুখের ভাবে আলেখ্যের নিজের চিত্তও করুণ হইয়া আসিল, কিন্তু সে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া প্রশ্ন করিল—ট্রেন এবং স্টীমারকে আপনি ভাল মনে করেন না?
বৃদ্ধ হাসিয়া ফেলিলেন। কহিলেন—কোন কিছুর ভাল-মন্দই কি এমন বিচ্ছিন্ন করে নির্দেশ করা যায় দিদি? আর সকলের সঙ্গে যুক্ত করে, সামঞ্জস্য করে তবেই তার ভাল-মন্দের সত্যকার বিচার হয়।
আলেখ্যও হাসিল, কহিল—ওটা শুধু আপনার কথার মারপ্যাঁচ। আসল কথা, আপনাদের পণ্ডিত-সমাজ বিলাতী শিক্ষার অত্যন্ত প্রতিকূলে। ওদের যা-কিছু সমস্তই মন্দ এবং আপনাদের যা-কিছু সমস্তই ভাল, এই আপনাদের বদ্ধমূল ধারণা। যতক্ষণ না তাদের বিদ্যা, তাদের বিজ্ঞান আপনারা আয়ত্ত করবেন, ততক্ষণ কোনমতেই নিরপেক্ষ বিচার করতে পারবেন না।
বৃদ্ধ ক্ষণকাল নতমুখে চিন্তা করিয়া চোখ তুলিয়া চাহিলেন, বলিলেন—দিদি, নিজের মুখে নিজের পরিচয় দিতে সঙ্কোচ বোধ হয়, কিন্তু তোমার কথায় মনে হয় যেন, আচরণে আমার আত্মগোপনের অপরাধ হচ্ছে। সেকালে আমি একজন বড় অধ্যাপক ছিলাম। অমরনাথ আমারই ছাত্র। আমার কাছ থেকেই সে এম. এ. পাস করে; তার সংস্কৃত শিক্ষার গুরুও আমি। তুমি যে বিদ্যা ও বিজ্ঞানের কথা বললে, তা আয়ত্ত করতে পারিনি, কিন্তু একেবারে অনভিজ্ঞ বললেও মিথ্যাভাষণের পাপ হবে।
কথাটা শুনিয়া আলেখ্য চমকিয়া উঠিল, তাহাকে কে যেন মারিল। সেই তাহার আরক্ত মুখের প্রতি বৃদ্ধ নিঃশব্দে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—আজ তুমি শ্রান্ত, তুমি উপরে তোমার ঘরে যাও দিদি, অমরনাথ কোন বিপদে যদি না পড়ে থাকে ত কাল এসে দু’জনে আবার দেখা করব। আমিও চললাম,—এই বলিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিয়া পুনশ্চ কি একটা যেন বলিতে গেলেন, কিন্তু সহসা আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। ( ‘মাসিক বসুমতী’, চৈত্র ১৩৩০ )
জাগরণ – ০৫
পাঁচ
পরদিন বাড়ি ফিরিয়া রে-সাহেব নয়ন গাঙ্গুলীর আত্মহত্যার বিবরণ শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। মেয়েকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া সোজা তাহাদের বাড়ি চলিয়া গেলেন। এতটা আলেখ্য আশা করে নাই। বিকালবেলা যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন মুখ তাঁহার কথঞ্চিৎ প্রসন্ন, তথাপি এ সম্বন্ধে চুপ করিয়াই রহিলেন। সেখানে কি বলিলেন, কি করিলেন, আলেখ্য তাহার কিছুই জানিতে পারিল না। সেদিনটা এইভাবেই কাটিল। পরদিন সকালে একখানা চিঠি হাতে করিয়া আসিয়া আলেখ্য পিতাকে কহিল—মিস্টার ঘোষ ইন্দুকে নিয়ে বোধ করি সন্ধ্যার ট্রেনেই এসে পৌঁছবেন।
কে, ঘোষ-সাহেব?
আলেখ্য মাথা নাড়িয়া বলিল—না, কমলকিরণ। ঘোষ-সাহেব এবং ইন্দুর মা বোধ হয় পাঁচ-ছ’দিন পরে আসবেন।
পিতা কহিলেন—আচ্ছা।
আলেখ্য কহিল—তাদের অভ্যর্থনার উপযুক্ত কিছুই বন্দোবস্ত করে উঠতে পারিনি।
পারনি? এই পাঁচ-ছ’দিনের মধ্যেও কি হতে পারবে না মনে হয়?
আলেখ্য পূর্বের মত মাথা নাড়িয়া কহিল, সম্ভব নয় বাবা—এই বলিয়া সে কিছুক্ষণ নিঃশব্দে থাকিয়া কহিল, একটা অত্যন্ত বিশ্রী কাণ্ড হয়ে গেছে বাবা, তুমি বোধ হয় শুনেচ? কি দুঃখের বিষয়।
সাহেব বলিলেন, হাঁ।
তাদের সম্বন্ধে কি কোনরকম ব্যবস্থা করলে বাবা?
না, বিশেষ কিছুই করা হয়নি—এই বলিয়া সাহেব নীরব হইলেন। মেয়েকে তিনি কোনদিনই তিরস্কার করেন নাই, বিশেষতঃ সমস্ত মরিয়া-ঝরিয়া গিয়া এই বৃদ্ধ বয়সে সংসারের সর্বপ্রকার বন্ধন যখন এই কন্যাটাতেই স্থিরতা লাভ করিয়াছে, তখন হইতে এই মেয়ের কাছেই আপনাকে তিনি ধীরে ধীরে শিশুর মত করিয়া তুলিয়াছেন। সে-ই তাঁহার সর্ববিষয়ে অভিভাবক। তাহার বিরুদ্ধে বা অমতে কাজ করার শক্তি তাঁহার স্বভাবতই তিরোহিত হইয়াছে।
আলেখ্য কহিল—উপযুক্ত ব্যবস্থা কেন করে এলে না বাবা?
সাহেব বলিলেন—মা, বিষয় তোমার। সমস্ত তোমার হাতে তুলে দিয়ে আমি ছুটি নিয়েছি, এর ভাল-মন্দর ভার তোমার। যা কর্তব্য, তা তুমিই করবে।
আলেখ্য করুণকণ্ঠে কহিল—যদি বুঝতে না পেরে কোন অন্যায় করি বাবা, তবুও কি তুমি তার প্রতিকার করবে না?
পিতা বলিলেন—আমিই কি বড় বুদ্ধিমান? অন্তত: সংসারে সে প্রমাণ ত আজও দিতে পারিনি মা। আর, না বুঝে অন্যায় যদি কিছু করেই থাক, যিনি বুদ্ধি দেবার মালিক, তিনিই তোমাকে তার নিবারণের পথ বলে দেবেন।—এই বলিয়া বৃদ্ধের সজল দৃষ্টি একমুহূর্তে খোলা জানালার বাহিরে গিয়া অকস্মাৎ কোন্ অনির্দেশ্য শূন্যতায় স্থিতিলাভ করিল। পিতার ঠিক এই ভাবটি আলেখ্য পূর্বে কখনও লক্ষ্য করে নাই—সে যেন অবাক হইয়া গেল। ছেলেবেলা হইতে তাঁহাকে সে ষোল-আনা সাহেব বলিয়াই জানে। ধর্মমত লইয়া তিনি আলোচনা করিতেন না, ঈশ্বরে ভক্তি-বিশ্বাস আছে কি নাই, এ কথাও কোনদিন প্রকাশ করিতেন না, এবং করিতেন না বলিয়াই লোকের ঘরে-বাহিরে তাঁহাকে অবিশ্বাসী বলিয়া ধারণা ছিল। অথচ, সাবেক দিনের ক্রিয়া-কর্ম ঠাকুর-দেবতার পূজা-অর্চনা সমস্তই অব্যাহত ছিল। এই জটিল সমস্যার সমাধান করিতে আলেখ্যের জননী ইহাকে ভয় এবং দুর্বলতা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন, আলেখ্যের নিজেরও তাহাতে সংশয় ছিল না, কিন্তু বৃদ্ধ পিতার আজ এই অদৃষ্টপূর্ব মুখের চেহারা চক্ষের পলকে যেন তাহাকে আর একটা দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিল।
আলেখ্য ধীরে ধীরে বলিল—তুমি বেঁচে থাকতে আমাকে এ-দায়িত্ব দিয়ো না বাবা।
কেন মা?
আমি আদেশ তোমার লঙ্ঘন করেছি।
বৃদ্ধ সবিস্ময়ে কন্যার মুখের প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কি আদেশ আলো? আমার ত কোন আদেশের কথাই মনে পড়ে না মা!
আলেখ্য অধোমুখে অঞ্চলের পাড়টা আঙুলে জড়াইতে জড়াইতে চুপ করিয়া রহিল।
পিতা কহিলেন—কৈ, বললে না যে?
আলেখ্য তথাপি কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া অভিমানরুদ্ধ-স্বরে আস্তে আস্তে বলিল—তবে এসে পর্যন্ত আমার সঙ্গে তুমি কথা কও না যে বড়? আমি ত এক শ’বার স্বীকার করছি, বাবা, আমি অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছি। কিন্তু স্বপ্নেও ভাবিনি, আমাকে তিনি এত বড় শাস্তি দিয়ে যাবেন। আমি তোমার কাছেও মুখ দেখাতে পারছি নে বাবা, আমি এদেশে আর থাকবো না।—এই বলিয়া সে ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।
সাহেব কাছে আসিয়া ধীরে ধীরে মেয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন,—কিছুই বলিলেন না। এমনিভাবে কিছুক্ষণ কাটিল, বোধ হয় মিনিট পাঁচ-ছয়ের বেশী নয়, কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যে তাহার দুর্বলচিত্ত বৃদ্ধ পিতার যে পরিচয় আলেখ্যের ভাগ্যে জুটিল, তাহা যেমন অভাবনীয়, তেমনি মধুর। এই বিশ বৎসর বয়েসের মধ্যে ইহার আভাস পর্যন্তও কখনও তাহার চোখে পড়ে নাই। আজ মায়ের জন্য তাহার ক্লেশ বোধ হইতে লাগিল, এত বড় মাধুর্যের কোন আস্বাদই তিনি জীবনে উপভোগ করিয়া যাইতে পারিলেন না। পিতা সমাজে কখনও যান নাই, উপাসনায় কোন দিন যোগ দেন নাই, ভগবৎ-বিশ্বাসহীন নাস্তিক বলিয়া মনে মনে জননীর যেমন ক্ষোভ ছিল, স্বামীর চিত্ত-দৌর্বল্যের জন্যও পরিচিত আত্মীয়বন্ধুজনের সমক্ষেও তাঁহার তেমনি লজ্জার কারণ ছিল। পিতার প্রতি আলেখ্যের স্নেহ ও প্রীতি সংসারে কোনও সন্তানের চেয়েই হয়ত কম ছিল না, কিন্তু পুরুষোচিত শক্তি, সামর্থ্য ও দৃঢ়তার অভাব এই রোগ-জীর্ণ নিরীহ লোকটির বিরুদ্ধে আরোপ করিয়া মায়ের নিকট হইতে একটা করুণ অশ্রদ্ধার ভাবই সে উত্তরাধিকারের মত পাইয়াছিল। সেই পিতাকে অকস্মাৎ আজ সে এক সম্পূর্ণ নূতন দিক হইতে লক্ষ্য করিবার অবকাশ পাইয়া ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় একেবারে বিগলিত হইয়া গেল। এমন করিয়া সে একটা দিনও তাঁহাকে দেখিবার সুযোগ পায় নাই। নানা লোকের নানা উক্তি ও বিভিন্ন মতামত দিয়া এই দিকটাই যেন তাহার চোখের সম্মুখে একেবারে আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া ছিল। আজ অনুশোচনায় ও আত্মধিক্কারে হৃদয় পূর্ণ করিয়া সে পিতার স্নেহস্পর্শের নীচে নিঃশব্দে বসিয়া ভাবিতে লাগিল, হয়ত পিতা নিজের মত দুর্বল ও শক্তিহীন জানিয়াই তাঁহার বহুদিনের আশ্রিত অতিবৃদ্ধ গাঙ্গুলীকে মনে মনে স্নেহ করিতেন, তাঁহার প্রতি এত বড় কঠিন অবিচার হইয়া গেল, তিনি নিবারণ করিতে পারিলেন না, তাই নীরবে তাঁহার শোকাচ্ছন্ন কন্যা-দৌহিত্রের কাছে গিয়া তেমনি নীরবে কি যে করিয়া আসিলেন, কাহাকেও জানিতে দিলেন না, অথচ এতবড় অন্যায় যাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হইল, তাহাকে একটি ক্ষুদ্র তিরস্কারেও লাঞ্ছিত করিলেন না, দুই বিভিন্ন দিকের সমস্ত ব্যথাই নির্বাক হইয়া নিজের বুক পাতিয়া গ্রহণ করিলেন।
অপরাধী কন্যাকে যে ভার, যে দায়িত্ব একদিন তিনি নিজের হাতে অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যাহার করিয়া আর তাহার লজ্জার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিলেন না। বাহিরের লোকের কাছে হয়ত ইহা দুর্বলতার নামান্তর বলিয়াই প্রতিভাত হইবে, কিন্তু আলেখ্য আজ তাহার নব-লব্ধ দৃষ্টি দিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাইল, কত বড় বিশ্বাস ও স্নেহের শক্তি ইহারই মধ্যে সহজে আত্মগোপন করিয়া আছে।
আলেখ্য অঞ্চলে চোখ মুছিয়া লইয়া মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—বাবা! সংসারের ভার আর যদি তুমি ফিরে নিতে না চাও, আমাকে কি তুমি পথ দেখিয়েও দেবে না?
সাহেব হাসিয়া কহিলেন—তুমি ত জান মা, সংসারযাত্রায় আমি দ্রুতপদে চলতে পারিনি—সকলের পিছনেই আমি পড়ে গেছি। সেই পিছনের পথটাই আমি কেবল দেখাতে পারি, কিন্তু সে ত সকলের মনোমত হবে না।
আলেখ্য কহিল—আমার হবে বাবা।
সাহেব বলিলেন—যদি হয় নিয়ো; কিন্তু নিতেই হবে, তা কোনদিন মনে করো না।
আলেখ্য ক্ষণকালমাত্র চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—আমরা সবাই মিলে যখন দৌড়ে চলেছিলাম, তখন কেন যে তুমি পেছিয়ে চলতে বাবা, আজ যেন তার আভাস পেয়েছি। এখন থেকে যেন তোমার পায়ের দাগ ধরেই চলতে পারি বাবা, আমাকে তুমি সেই আশীর্বাদ কর।
সাহেব হাসিয়া তাহার মাথায় আর একবার হাত বুলাইয়া দিয়া শুধু কহিলেন—পাগলি! এই বুড়োর সঙ্গে কি তোরা চলতে পারবি মা? সে ধৈর্য কি তোদের থাকবে?
আলেখ্য বলিল—তোমাকে দেখে আজ এই কথাটাই সবচেয়ে বেশী মনে হচ্ছে বাবা, কেবল দৌড়ে বেড়ানোই এগোনো নয়। তাই, তুমি যখন ধীরে ধীরে পা ফেলে চলতে, আমরা সবাই ভাবতুম, তুমি পেছিয়ে পড়ছ। আজ থেকে তোমার পায়ের চিহ্নই যেন সকল পথে আমার চোখে পড়ে।
সাহেব স্থির হইয়া রহিলেন। কিন্তু সে হাতখানি তাঁহার তখনও আলেখ্যের মাথার ’পরে ছিল, সেই পাঁচ আঙুলের স্পর্শ দিয়া যেন পিতার অন্তরের আশীর্বাদ কন্যার সর্বাঙ্গে ক্ষরিয়া পড়িতে লাগিল।
খানিকক্ষণ এমনি নিঃশব্দে কাটিবার পরে আলেখ্য কহিল—বাবা, কাল তোমার খুড়ো-মশাই এসেছিলেন।
খুড়ো-মশাই? সাহেব সবিস্ময়ে কন্যার প্রতি চাহিলেন।
কন্যা কহিল—ছেলেবেলায় তাঁকে তুমি এই বলে ডাকতে। পণ্ডিত ব্রাহ্মণ। নিমাই ভট্টাচায্যি নাম।
সাহেব অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তিনি বেঁচে আছেন? এত বড় আসল মানুষ সহজে মেলে না, মা। তাঁর কোনরূপ অমর্যাদা হয়নি ত?
আলেখ্য মাথা নাড়িয়া জানাইল, না। কহিল, তিনি এসেছিলেন আমার পরিচয় নিতে এবং তাঁর ছেলেবেলায় এই ঐশ্বর্যময়ী বাংলাদেশে যে কত ঐশ্বর্য ছিল তার পরিচয় দিতে। সে কি আশ্চর্য ছবি বাবা! ফুলে-ফলে, শস্যে-ধানে, শোভায়-স্বাস্থ্যে কি সম্পদই না এদেশের ছিল! আমার ভুলের সীমা নেই; আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত নেই,—এ কথা আমি স্বপ্নেও অস্বীকার করিনে, কিন্তু আমার মত একটা সামান্য মেয়ের অন্যায়ের ফলে যে-দেশে এত বড় মর্মান্তিক ঘটনা ঘটতে পারে, তাকে নিবারণ করবার কোন সম্বল যে-দেশের হাতে নেই, সর্বরকমে কাঙাল করে যারা এই সোনার দেশকে এতবড় নিঃস্ব-নিরুপায় করে তুলেছে, তাদের অপরাধেরই কি অবধি আছে বাবা?
সাহেব গভীর নিশ্বাস মোচন করিয়া কহিলেন—হুঁ। তখনকার দিনে উপবাসের ভয়ে যে তাঁকে আত্মহত্যা করতে হত না, সে ঠিক। চাকরি গেলেও তাঁরা না খেয়ে মরতেন না। গ্রামের মধ্যে দু’মুঠো অন্ন তাঁদের জুটতো।
আলেখ্য বলিল,—অক্ষম অপারক বলে আমার ভুল ত সে থেকে তাঁকে বঞ্চিত করতে পারত না! এবং এত বড় কলঙ্কের ছাপ ত সে–দিনে আমার কপালেও ছাপ মেরে যেত না!—এই বলিয়া সে ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া পুনশ্চ রুদ্ধকণ্ঠে বলিতে লাগিল, বাবা, তোমরা সবাই বলো, পৃথিবী সম্পদে সভ্যতায় দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে এবং এই বাঙলাদেশে আমরাই তাদের অগ্রদূত,—নিমাই ভট্চায্যি তাই আজ আমাকে দেখতে এসেছিলেন, কিন্তু এত বড় তামাশা কি আর আছে? গাঙ্গুলী-মশায়ের পীড়িত উদ্ভ্রান্ত আত্মার কল্যাণ হোক, কিন্তু যে সভ্যতায় দরিদ্রের মুখের গ্রাস, দুঃখীর জীবন ধনীর মুঠোর মধ্যে এমন ভয়ানক নিরুপায় করে এনে দেয়, তাকে কেউ রক্ষে করতে পারে না, সে কি-রকম সভ্যতা? আর তাই যদি হয় বাবা, এ সভ্যতায় আমার কাজ নেই। এই নির্দয় প্রহসন থেকে আমার মুক্তি চাই।
পিতা মুখ তুলিয়া চাহিলেন। কন্যার বেদনাতুর হৃদয়ের ক্ষুব্ধ উত্তেজনাকে শান্ত করিতে নিজেও শান্তকণ্ঠে কহিলেন—উপায় কি মা? দুঃখী-দরিদ্র চিরদিনই ধনীর হাতের মধ্যে থাকে আলো, এমনিই সংসারের বিধান।
আলেখ্য শান্ত হইতে পারিল না, কহিল—না বাবা, এ বিধান যতই পুরানো, যতই কেননা চিরদিনের হউক, কিছুতেই ভাল না। জগতে ধনী ও দরিদ্র যদি থাকে ত থাক, কিন্তু এমন একান্তভাবে, এমন উপায়হীন কঠিন বাঁধনে কেউ কারও হাতের মধ্যে থাকা কোনমতেই মঙ্গলের বিধান হতে পারে না বাবা। ধনীরও না, দরিদ্রেরও না। এতটুকু মুঠোর চাপে যার মানুষ মারা পড়ে, অন্ততঃ, সে কিছুতেই বলতে পারে না। লোকে বলে, তার মাথা ঠিক ছিল না, তবু ত আমি এ কথাটাও জীবনে ভুলতে পারব না যে, তার পাঁচ বৎসরের আয়ু আমার ঐ একটা আয়নার মধ্যেই রয়ে গেছে। আরও কত লোকের মরণ-ইতিহাস যে আমার জুতো-জামার পরতে পরতে লেখা আছে, তাই বা কে জানে বাবা?
তাহার কথা শুনিয়া বৃদ্ধ পিতা ভয় পাইলেন; জোর করিয়া একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—পাগল আর কি! তা হলে ত সংসারে আর বাস করা চলে না আলো!
আলেখ্য জবাব দিল—তোমার কপালে ত বুড়োমানুষের রক্তের দাগ নেই বাবা।
পিতা কহিলেন—তোমার যত দোষ এঁরা তোমাকে বুঝিয়ে গেছেন মা, তার সবই সত্য নয়।
মেয়ে বলিল—আমি কি এর দাগ মুছতে পারব না বাবা?
বাবা বলিলেন—কেন পারবে না? তোমার কোন কাজেই ত আমি বাধা দিইনে মা।
রূপার রেকাবিতে একখানা হলদে রঙের খাম রাখিয়া বেহারা আসিয়া উপস্থিত হইল। আলেখ্য খুলিয়া দেখিয়া পিতার হাতে দিয়া কহিল—ইন্দুকে নিয়ে কমলকিরণ আসছেন।
কখন?
আজই সন্ধ্যার ট্রেনে।—এই বলিয়া আলেখ্য অন্যত্র চলিয়া গেল।
সে চলিয়া গেলে রে-সাহেব সেইখানে বসিয়াই নানা কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই অত্যন্ত শোকাবহ ঘটনার সুতীব্র আঘাতে আলেখ্যের মনের মধ্যে যে ঝড় বহিতে শুরু করিয়াছে, তাহার গুরুত্ব কত এবং কতখানি ব্যাপক হইয়া জীবনকে তাহার অধিকার করিবে, এবং সমাজের মধ্যে ইহার ফলাফল কি, তাহাই উদ্বিগ্নচিত্তে মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন।
যে ক্ষুদ্রায়তন সঙ্কীর্ণ সমাজের মাঝে তাঁহার জীবনের দীর্ঘকাল কাটিয়া গেল, তাহার প্রতি তাঁহার মমতা ও প্রীতি ধীরে ধীরে যে কমিয়া আসিতেছিল, এ কথা তিনি মুখ ফুটিয়া ব্যক্ত না করিলেও নেতৃস্থানীয়গণের অগোচর ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া মেয়ের সম্বন্ধে এমন কথা কখনও তিনি কল্পনাও করিতেন না যে, যে সমাজ ও সংস্কারের মধ্যে দিয়া সে বড় হইয়া উঠিয়াছে, তাহাকেই অশ্রদ্ধা করিয়া সে কিছুতেই সুখী হইতে পারে! এ আশ্রয় হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া তাহার কোনমতেই চলিতে পারে না। এ বিশ্বাস তাঁহার দৃঢ় ছিল। ঘোষ-সাহেব ও তাঁহার পারিবারিক চালচলনের প্রতি মনে মনে তাঁহার অতিশয় বিরাগ ছিল, কন্যার প্রতি ইহাদের দৃষ্টি আছে, এ কথা মনে করিয়াও মনের মধ্যে তাঁহার জ্বালা করিত; কিন্তু আজ তাহাদের আসার সংবাদে তিনি শুধু খুশী নন, যেন নিশ্চিন্ত হইলেন। ইন্দুমতী আলেখ্যের ছেলেবেলার বন্ধু এবং কমলকিরণও যে অবাঞ্ছিত অতিথি নয়, এ ধারণা তাঁহার ছিল। সম্প্রতি যে অঘটন ঘটিয়া গেছে, যাহাকে ফিরাইবার আর পথ নাই, তাহাকেই কেন্দ্র করিয়া সমস্ত গ্রামের মধ্যে যে গ্লানি ও শোকোচ্ছ্বাসের তুফান ছুটিয়াছে, তাহারই ধাক্কা হইতে মেয়েটা যদি কিছুদিনের জন্যও নিষ্কৃতি পায়, ব্যাপারটাকে যদি দুটা দিনও ভুলিয়া থাকিতে পারে, এই মনে করিয়া সাহেব আগে হইতেই তাঁহার অতিথিদের অন্তরের মধ্যে সংবর্ধনা করিলেন। সেইদিন সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বে ভগিনীকে লইয়া কমলকিরণ আলেখ্যের পৈতৃক বাসভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সাহেব নিজে থাকিয়া তাঁহাদের আদর করিয়া গ্রহণ করিলেন। আলেখ্য পাশে দাঁড়াইয়া সভ্য-সমাজের সর্বপ্রকারে অনুমোদিত অভ্যর্থনার কোথাও কোন ত্রুটি করিল না, কিন্তু তবুও তাহার মুখের চেহারায় আগন্তুক এই দুটি ভাই-বোনে কি যে সহসা দেখিতে পাইল, তাহাদের মন যেন একেবারে দমিয়া গেল।
বাহিরে তাহার প্রকাশ নাই, রাত্রে ডিনারের আয়োজন একটু বিশেষ করিয়াই হইল।
মুসলমান বাবুর্চির এত দিন প্রায় একরকম ঘুমাইয়া কাটিতেছিল, সে তাহার যথাসাধ্য করিল। ফুলের সময় নয়, তথাপি টেব্লে তাহার অপ্রতুল হইল না, প্রয়োজনের অনেক বেশী আলো জ্বলিল, সদ্য-রং-করা দেওয়ালের গায়ে ও সাহেব-বাড়ির দীর্ঘায়তন মুকুরে তাহার সমস্ত রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া ঘরটাকে যেন দিনের বেলা করিয়া দিল।
রূপার ছুরি-কাঁটা, রূপার চামচ, রৌপ্যের বাতিদান, দুর্মূল্য পাত্রে দুর্মূল্য ভোজ্য ও পেয়, তুষারশুভ্র চাদরের উপরে সে যেন কেবল চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিবার। সজ্জায় ও শোভায়, পোশাক ও পরিচ্ছদে, হাসি ও গল্পে, বিলাস ও ব্যসনে মনে হইল, যেন একটা দুঃখ ও পীড়নের ভূত সহসা গয়ায় পিণ্ডলাভ করিয়া এই একটা বেলার মধ্যেই বাড়িটাকে ছাড়িয়া গিয়াছে।
ডিনার অগ্রসর হইয়া চলিল। অজীর্ণ-রোগগ্রস্ত রে-সাহেবের উৎসাহে, তাঁহার ছুরি ও কাঁটার ক্ষিপ্র পরিচালনে হঠাৎ যেন তাঁহাকে চেনাই যায় না। ঠিক এমনই সময়ে বেহারা আসিয়া তাঁহার হাতে একটুকরা কাগজ দিল। চশমার অভাবে তিনি হাত বাড়াইয়া কাগজটুকু ইন্দুর হাতে দিয়া বলিলেন—দেখ ত মা কে?
ইন্দু পড়িয়া কহিল, অমরনাথ।
সাহেব অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া বলিলেন—ফিরেছে সে? আমি কতই না ভাবছিলাম।—কমলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, সে আমাদের বাড়ির ছেলের মত। ঝড়ু, তাকে এইখানেই ডেকে নিয়ে আয়।
আলেখ্য শঙ্কিত হইয়া কহিল—এই ঘরে?
সাহেবের সেদিকে চোখ ছিল না, বলিলেন—হ’লই বা। কমল, এমন একটি ছেলে কিন্তু বাবা, আর কখনও চোখে দেখনি। আমাদের মধ্যে ত ছেড়েই দাও, হয়ত বিলেতেও কখনও দেখতে পাওনি। যা না ঝড়ু, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?
ঝড়ু চলিয়া গেল এবং অনতিকাল পরেই লোকটিকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া উপস্থিত হইল। তাহার খালি পা, মুখ অতিশয় শুষ্ক ও মলিন, মনে হয় যেন সমস্তদিন তাহার জলবিন্দুটুকুও জুটে নাই, মাথার একদিকে ব্যান্ডেজ করা—রক্তের দাগ তখনও কালো হইয়া আছে, সাহেব চমকিয়া উঠিলেন,—ব্যাপার কি অমরনাথ—এ কি কাণ্ড?
আগন্তুক চারিদিকে নিঃশব্দে বার বার দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। ভোজনে ক্ষণকালের জন্য তাঁহাদের বাধা পড়িল বটে, কিন্তু দরিদ্র, মূর্খ, ক্ষুধিত, বঞ্চিত এই পল্লীর মাঝখানে এই আহারের আয়োজন তাহার কাছে যেন বিড়ম্বনা একেবারে মূর্তিমান হইয়া দেখা দিল। (‘মাসিক বসুমতী,’ বৈশাখ ১৩৩১)।
জাগরণ – ০৬
ছয়
অত্যন্ত কৌতূহলে ভয় ও ভাবনা মিশিয়া সাহেবের আহারের রুচি ও প্রবৃত্তি মুহূর্তে তিরোহিত হইয়া গেল। হাতের কাঁটা ও ছুরি ফেলিয়া দিয়া চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন—এ-সব কি করে হল অমরনাথ?
অমরনাথ কহিল—আপনি কোন্টা জানতে চাইছেন?
সাহেব ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন—তুমি কি রাগ করলে বাবা? আমি সমস্ত ব্যাপারটাই জানতে চাইচি। কিন্তু সে না হয় পরে হবে, তোমাকে আঘাত করলে কে? পুলিশ?
অমরনাথ ঘাড় নাড়িয়া কহিল—না, গ্রামের লোকই আঘাত করেছে, কিন্তু এই যে ঠিক সত্য, তাও নয় রায়-মশায়।
তা হলে সত্যটা কি?
অমরনাথ বলিল—দেখুন, এর মধ্যে সত্য শুধু এইটুকু যে, আমার ফোঁটা – কয়েক রক্তপাত হয়েছে।
সাহেব ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—কিন্তু এ কাজ আমার হাটের মধ্যেই ত হল।
অমরনাথ নীরবে সায় দিয়া জানাইল—তাই বটে।
এখনও তোমার খাওয়া-দাওয়া বোধ করি কিছুই হয়নি?
না।
সাহেব বলিলেন—তোমার বাড়ি ত খুব কাছে নয়,—কিন্তু এ বাড়িতেও উদ্যোগ আয়োজন বোধ হয় কিছুই হতে পারবে না। এখানে তুমি কিছুই খাবে না, না?
অমরনাথ একটুখানি হাসিয়া বলিল—না।
সারাদিনটা তা হলে উপবাসেই কাটলো?
অমরনাথ ইহার উত্তর কিছুই দিল না, কিন্তু বুঝা গেল, সমস্ত দিনটা তাহার উপবাসেই কাটিয়াছে। সাহেব নিশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন, তা হলে আর বিলম্ব করো না, বাবা, বাড়ি যাও।—এই বলিয়া তিনি সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—চল, তোমাকে একটুখানি এগিয়ে দিয়ে আসি।
অমরনাথ ব্যস্ত হইয়া উঠিল, কহিল—সে কি কথা? আমাকে আবার এগিয়ে দেবেন কি! তা ছাড়া, খাওয়া আপনার শেষ হয়নি,—উঠতে আপনি কিছুতে পারবেন না, রায়-মশায়।
সাহেব জিদ করিলেন না, কোন বিষয়েই জিদ করা তাঁহার স্বভাব নয়। শুধু যাইবার সময় ধীরে ধীরে বলিলেন—যেজন্যে তুমি এত রাত্রে এসেছিলে, তার আভাসমাত্র পাওয়া ভিন্ন আর কিছুই জানতে পারলাম না। কিন্তু কাল যখন হোক একবার এসো, অমরনাথ।
অমরনাথ স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিলে সাহেব কহিলেন—এ অঞ্চলে অমরের গায়ে কেউ আঘাত করতে সাহস করবে, এ কথা সহজে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না। ভিতরে ভিতরে ব্যাপারটা হয়ত অনেক দূর এগিয়ে গেছে। তা ছাড়া আমারই হাটের মধ্যে এ দুর্ঘটনা ঘটলো!
ভাবে বুঝা গেল, রে-সাহেবের আহারে আর প্রবৃত্তি নাই, আলেখ্য বিমর্ষ অধোমুখে খাদ্যবস্তু লইয়া খাওয়ার ভান করিতে লাগিল মাত্র। মিনিট দশ-পনর পূর্বেও ডিনারের যে উৎসব পূর্ণ উদ্যমে চলিয়াছিল, ঐ অপরিচিত লোকটার আসা ও যাওয়ার মধ্যেই সমস্ত যেন নিরুৎসাহে নিবিয়া গেল। তাহার কথাবার্তা সংক্ষিপ্ত এবং প্রাঞ্জল, এমনকি, হিন্দুত্বের গোঁড়ামির দিক দিয়া একপ্রকার সরল রূঢ়তাও আছে, অনাড়ম্বর বেশভূষা একটু বিশেষ করিয়াই চোখে পড়ে, সম্প্রতি একটা মারামারি করিয়া আসিয়াছে এবং তাহা পুলিশের বিরুদ্ধে হইলে এক ধরনের বীরত্বও আছে। কিন্তু রে-সাহেবের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার হেতু ইন্দু বা তাহার দাদা সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করিতে পারিয়া ইন্দুই প্রথমে প্রশ্ন করিল—ইনি কে, আলো?
রে-সাহেব ইহার জবাব দিলেন; কহিলেন—ইনি একজন নবীন অধ্যাপক, টোলে অধ্যাপনা করেন, গুটিকয়েক বিদেশী ছাত্রও আছে, কিন্তু অধ্যাপনার কাজ এখন বিরল হয়ে এলেও এদেশে আরও অধ্যাপক আছেন, সুতরাং এ তাঁর বিশেষত্ব নয়; অধুনা দেশের কাজে লেগে গেছেন, কিন্তু একেও অসাধারণ বলিনে। অসাধারণত্ব যে এঁর ঠিক কোথায় তাও আমি জানিনে, কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণী আমি নিঃসংশয়ে করে যেতে পারি, ইন্দু, অমরনাথ বেঁচে থাকলে একদিন এঁকে মানুষ বলেই দেশের মানুষকে স্বীকার করতে হবে।
কাহারও ভবিষ্যদ্বাণীর উপরে তর্ক করা চলে না, বিশেষতঃ তিনি গুরুজনস্থানীয় হইলে নীরব হইতেই হয়। ইন্দু চুপ করিয়া রহিল; কমলকিরণ প্রশ্ন করিল—মিস্টার রে, এই লোকটাই কি আপনার প্রজাদের উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছিলেন?
সাহেব মাথা নাড়িয়া বলিলেন, হাঁ।
আপনার হাটের মধ্যে ইনি গিয়েছিলেন কেন? বোধ করি এই উদ্দেশ্যেই?
সাহেব প্রশ্ন শুনিয়া হাসিলেন; কহিলেন—বিলাতী কাপড়ের বিক্রি বন্ধ করতে।
কমল কহিল—অর্থাৎ নন্-কো-অপারেশনের ভিলেজ পাণ্ডা। দোকানদারের দল বিরক্ত হয়ে তাই নবীন অধ্যাপকের রক্তপাত করেছে, এই না মিস্টার রে?
সাহেব সায় দিয়া বলিলেন—খুব সম্ভব তাই।
কমল কহিল—এবং তারা খবর দিয়ে পুলিশ এনে হাজির রেখেছিল?
আলেখ্য এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল, সে-ই ইহার উত্তর দিল, সলজ্জ মৃদুকণ্ঠে বলিল—আমিই একদিন পুলিশের সাহায্য চেয়ে ম্যাজিস্ট্রেটকে চিঠি লিখে দিয়েছিলাম।
কমল কহিল—ঠিক কাজ করেছিলেন, এখন শুধু এইটুকু বাকী আছে—লোকটিকে প্রসিকিউট করা। অন্তত: মার্কেট আমার হলে আমি তাই করতাম।
সাহেব কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেদিনের হরতালের কথা মনে পড়িল, যেদিন রাগ করিয়া রাস্তার লোক কমলের পিতার গাড়ির কাচ ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। এ অপরাধ তিনি ক্ষমা করেন নাই, অনেককেই কারাগারে যাইতে হয়েছিল। ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া শেষে কহিলেন—আমার মনে হয়, তাতে লাভের চেয়ে লোকসানের মাত্রাই বেশী হত কমল। হয়ত কাল কিংবা পরশু আমাদের যাকে হোক হাটের একটা ব্যবস্থা করতে যেতেই হবে, সহজে মীমাংসা হবে না,—অথচ পুলিশের লোক মধ্যে না থাক্লে মনে হয়, এর প্রয়োজনই হত না।
ইন্দু কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে খবর দেওয়া কি আপনার মত নিয়ে হয়নি?
সাহেব কন্যার অধোমুখের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া কহিলেন—আমার মতামতের আবশ্যকই ছিল না, ইন্দু। তোমরা একটা কথা জান না যে, সাংসারিক সকল ব্যাপার থেকেই আমি অবসর নিয়েছি, বিষয় এখন আলোর, বিলি-ব্যবস্থা যা-ই করতে হোক, তাকেই করতে হবে। ভুল যদি হয়েও থাকে, তাকেই এর সংশোধনের ভার নিতে হবে।
কমল চকিত হইয়া বলিল—আপনি জীবিত থাকতে সে কি করে হতে পারে?
সাহেব হাসিমুখে কহিলেন—তা হলে আমি বেঁচে নেই, এই কথাই মনে করে নিতে হব।
কমল বলিল—মনে করা কঠিন এবং আলেখ্যের মত অনভিজ্ঞের এ ভার বহন করা আরও বেশী কঠিন।
ইন্দু বলিল—বিস্তর ভুলচুক হবে।
সাহেব কহিলেন—ভুলচুকের দণ্ড আছে। হলে নিতে হবে।
ইন্দু কহিল—তা ছাড়া বিপদ বাধাবার শত্রু যখন আশেপাশে রয়েছে।
সাহেব কহিলেন—আশেপাশে শত্রুই শুধু থাকে না, ইন্দু, মিত্রও থাকে। তারা বিপদ-উদ্ধারের পথ দেখিয়ে দেবে। সে যার থাকে না, সংসারে সে পরাভূত হয়। একাকী বাপ তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না, মা।
ইন্দু তাহা স্বীকার করিল এবং তাহার দাদা ইহাকে প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত মনে করিয়া মৌন হইয়া রহিল।
পরদিন সকালেই রে-সাহেবের অনুজ্ঞামত অমরনাথ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রাতরাশ সেইমাত্র শেষ হইয়াছে, বসিবার ঘরে সকলে আসিয়া উপবেশন করিলে সাহেব যে কথাটা সর্বপ্রথম জানিতে চাহিলেন, তাহা লোকটার নাম, যে হাটের মধ্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল।
অমরনাথের মুখের ভাবে বিস্ময় প্রকাশ পাইল, জিজ্ঞাসা করিল—কেন?
সাহেব বলিলেন—এর একটা প্রতিকার হওয়া চাই।
অমরনাথ কহিল—কিন্তু আপনি ত আর কিছুর মধ্যেই নেই, রায়-মশায়।
সাহেব বলিলেন—আমি নেই সত্য, কিন্তু যিনি আছেন, তাঁর ত এ বিষয়ে কর্তব্য আছে।
পিতার ইঙ্গিত আলেখ্য বুঝিল। নয়ন গাঙ্গুলীর আত্মহত্যার পর হইতে সে গ্রামের লোকজনের সম্মুখে সহজে আসিতে চাহিত না, আসিয়া পড়িলেও নীরব হইয়াই থাকিত। তাহার সর্বদাই মনে হইত, ইহারা এই দুর্ঘটনায় তাহাকেই সর্বতোভাবে দায়ী করিয়া রাখিয়াছে এবং অন্তরালে যে-সকল কঠিন ও কটু বাক্য তাহারা উচ্চারণ করে, কল্পনায় সমস্তই সে যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইত; এবং ইহার লজ্জা তাহাকে যে কতদূর আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা শুধু সে নিজেই অনুভব করিত।
আলেখ্য পিতার প্রশ্নের সূত্র ধরিয়া বলিল, বেশ, আমিই আপনাকে তাদের নাম জানাতে অনুরোধ করছি।—এই বলিয়া আজ সে অনেকদিনের পরে মুখ তুলিয়া চাহিল। সেই শান্ত, বিষণ্ণ মুখের প্রতি অমরনাথ তীক্ষ্ণদৃষ্টি পাতিয়া ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিল—দেখুন, তারা আপনার প্রজা, কেবলমাত্র কৌতূহলবশেই যদি তাদের পরিচয় জানতে চেয়ে থাকেন, এ কৌতূহল আপনাকে দমন করতে হবে।
আলেখ্য কহিল—তারা আমার প্রজা না হলে আপনাকে আমি জিজ্ঞাসাও করতাম না। জমিদারের একটা কর্তব্য আছে, এই অন্যায়ের আমি প্রতিকার করতে চাই।
অমরনাথ বলিল,—আপনি তাদের শাস্তি দিতে চান, কিন্তু তাতে প্রতিকার হবে না।
আলেখ্য কহিল—অন্যায়ের প্রতিকার ত শুধু শাস্তি দিয়েই হয়।
অমরনাথ মুচকিয়া হাসিয়া কহিল—এই নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনে এবং জমিদার কি করে প্রজার শাসন করে থাকেন, তাও আমি জানিনে। কিন্তু এ কথা নিশ্চয় জানি, অন্যায় এবং অজ্ঞতা এক জিনিস নয় এবং শাস্তি দিয়েও এর কিছু প্রতিকার হবে না।
একমুহূর্ত স্থির থাকিয়া অমরনাথ পুনশ্চ কহিল, আমাকে তারা আঘাত করেছে সত্য, কিন্তু সেই আঘাতের শাস্তি দিতে যাওয়ার মত পণ্ডশ্রম আর নেই। মার খাওয়াটাই যদি আমার কাছে বড় হত, সেখানে আমি যেতাম না। আমার আঘাতে যথার্থই যদি আপনি বিচলিত হয়ে থাকেন ত এইটুকু প্রার্থনা আমার মঞ্জুর করুন, এই নিয়ে আমার প্রতি তাদের আর বিরূপ করে তুলবেন না।—এই বলিয়া অমরনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল।(‘মাসিক বসুমতী,’ আষাঢ় ১৩৩১)।
জাগরণ – ০৭
সাত
রে-সাহেব কমলকিরণকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন—এ সম্বন্ধে তোমার কি মত হে?
কমলের চোখের দৃষ্টি চোখের পলকে ইন্দু ও আলেখ্যের মুখের উপর দিয়া গিয়া সাহেবের প্রতি স্থির হইল।
অমরনাথ গমনোদ্যত হইয়াও তখনও দাঁড়াইয়া ছিল; নিজের পূর্ব-কথার অনুবৃত্তিস্বরূপে বিনীতকন্ঠে কহিল—সম্পত্তি আপনাদের, এর ভালমন্দ আপনাদেরই নিরূপণ করতে হবে, কিন্তু যাই করুন, আমাকে উপলক্ষ করে যেন কিছুই করবেন না, এই আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ।
সাহেব ব্যস্ত হইয়া বলিতে গেলেন—না না, তুমি যখন তা চাও না, কি বল ইন্দু? কি বল আলো? এই বলিয়া তিনি উপস্থিত সকলকে, বিশেষ করিয়া যেন নিজেকেই নিজে আবেদন করিলেন।
ইন্দু ঘাড় নাড়িল, কমলকিরণও বোধ হয় যেন সায় দিতে যাইতেছিল এবং আলেখ্য ত গাঙ্গুলী বৃদ্ধের আত্মঘাতের ভারে চাপা পড়িয়াই ছিল—স্বাধীন মতামত দিবে কি, প্রকাশ্যে মুখ দেখাইতেও সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল, কিন্তু হঠাৎ উত্তর বাহির হইল তাহারই মুখ দিয়া। এই নবীন অধ্যাপকের সহিত প্রথম পরিচয়ের দিনে তাহাদের সদ্ভাব জন্মে নাই; তাহার পরে যতবারই উভয়ের সাক্ষাৎ ঘটিয়াছে, অসদ্ভাব বৃদ্ধির দিকেই বরাবর গিয়াছে। গাঙ্গুলীর মৃত্যুর ব্যাপারে সেদিন রাত্রে অমরনাথের কাছে সে সহানুভূতি পাইয়াছিল, বিরুদ্ধতা সে করে নাই, তথাপি আলেখ্যের মনের লজ্জা তাহাতে গোপনে বাড়িয়াছিল বৈ লেশমাত্র কমে নাই; এবং ইহারই সম্মুখে আপনাকে যেন সে সামান্য, একাকী ও সর্বাপেক্ষা বেশী অপরাধী না ভাবিয়া পারিত না। আজ এইসকল পরিচিত বন্ধুদের মধ্যে বসিয়া অকস্মাৎ আপনাকে যেন সে ফিরিয়া পাইল। বেশ সহজভাবে মুখ তুলিয়া স্বাভাবিক শান্তস্বরে বলিল—হাঙ্গামা বাধালেন আপনি, আর বিপদ ভোগ করব শুধু আমরা? এ কি-রকম প্রস্তাব হ’ল আপনার?
কমলকিরণ সজোরে মাথা নাড়িয়া বলিল—একজ্যাক্ট্লি! ঠিক তাই আমি বলি।
অমরনাথ পা বাড়াইয়াছিল, থমকিয়া দাঁড়াইল।
আলেখ্য কহিল—আপনার বাড়ি এখানে, আপনি গেছেন আর একটা জায়গায় হাটের মধ্যে মেড্ল করতে। জানিনে, তাতে দেশের ভাল হবে কি মন্দ হবে। ধরে নিলাম, ভালই হবে, কিন্তু সম্পত্তি আমার, তার ভালমন্দতে আমারও একটু শেয়ার আছে। অথচ, আমার অভিমতের কোন মূল্য আপনার কাছে নেই, এখানে আমাকেই বলতে এসেছেন, আপনাকে যেন না উপলক্ষ সৃষ্টি করি। এ অনুরোধ আপনার নিতান্ত অসঙ্গত।
তাহার মুখের এই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত মন্তব্য শুনিয়া শুধু কেবল তাহার শ্রোতাই নয়, উপস্থিত সকলেই যেন অবাক্ হইয়া গেল। সবচেয়ে বেশী হইলেন রে-সাহেব নিজে।
বিস্মিত অমরনাথ আলেখ্যের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, সুসঙ্গত উত্তর সহসা তাহার মুখে যোগাইল না।
সাহেব কি একটা বলিতে চাহিয়া শুধু বলিলেন—না না, ঠিক তা নয়—কিন্তু কি জান, অমরনাথ বোধ করি—
আলেখ্য হাসিয়া কহিল—কি বোধ কর বাবা?
ইন্দু এবং কমলকিরণ দুইজনেই মুখ টিপিয়া হাসিল।
অমরনাথ আপনাকে লাঞ্ছিত বোধ করিয়া কহিল,—বেশ, আমার অনুরোধ আপনি রাখবেন না।
আলেখ্য কহিল—অনুরোধ রাখব না, এ আমি বলিনি। কিন্তু ন্যায়-অন্যায় যাই হোক, কেবলমাত্র তারা আপনার প্রতি আর বেশী অপ্রসন্ন না হয়, এই অসঙ্গত অনুরোধ আমি রাখব না বলেছি।
অমরনাথ কহিল—কোনরূপ অনুরোধ করার সঙ্কল্প নিয়ে আপনাদের কাছে আমি আসিনি। আমাকে তারা আঘাত করেছে, কিন্তু এই নিয়ে তাদের শাস্তি দিতে যাবার মত নিরর্থক কাজ আর নেই, এই কথাই শুধু আমি জানাতে এসেছিলাম।
আলেখ্য বলিল—একজন তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষে যা নিরর্থক, জমিদার এবং প্রজার পক্ষে তা নিরর্থক না-ও হতে পারে। অন্তত:, সে স্থির করবার ভার আমাদের উপরেই থাক।
কমলকিরণ কহিল—ঠিক তাই। আমাদের রেস্পন্সিবিলিটি আমরা নিজেদের হাতেই রাখবো। থার্ড পারসনের মাঝখানে আসবার একেবারেই প্রয়োজন দেখিনি। মিস্টার রে, আপনি কি বলেন?
সাহেব সকলের মুখের দিকেই চাহিলেন। এই কালই ত আলেখ্য বাঙলাদেশের দরিদ্র প্রজাদের দুঃখে বিগলিত হইয়া কত কথাই বলিয়াছিল এবং অমরনাথ যে তাহাদেরই কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, এ কথাও ত সে জানে।
আঘাত খাইয়া যে প্রতিঘাত করিতে চাহে না, তাহাদেরই কল্যাণের জন্য যে নিঃশব্দে সমস্ত সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার সহিষ্ণুতায় হঠাৎ কেন যে আর একজন এতখানি অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। তিনি এদিকে-ওদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিলেন—এ ত অতিশয় সাধারণ আলোচনা কমল, এর ভিতর হিট্ কিসের জন্য উঠছে, আলো? বেশ ত, কি করা উচিত অনুচিত, শান্ত হয়েই তোমরা তার বিচার কর না, অমরনাথ! আর এখনই বা কেন? কালও হতে পারে।
অমরনাথ কহিল—রায়-মশায়, তৃতীয় ব্যক্তির মাঝখানে আসাটা কেউ পছন্দ করে না। সংসারে জমিদার ও প্রজা ছাড়া যদি না আর কিছু থাকতো ত কোন কথাই ছিল না, কিন্তু বিপদ এই যে, তৃতীয় ব্যক্তি বলে একটা বস্তু সংসারে আছে, এবং পছন্দ না করলেও ও-বস্তুর অস্তিত্ব দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত করা যাবে না। এঁরা এত বোঝেন, এই তুচ্ছ কথাটাও যদি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতেন!—এই বলিয়া সে শুষ্ক হাস্য করিবার একটুখানি প্রয়াস করিলেও কথাগুলা যে পরিহাস নয়, বিদ্রূপ, তাহা বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইল না; এবং ইহার মধ্যে খোঁচা যাহা ছিল, তাহা বিদ্ধ করিতেও ত্রুটি করিল না।
আলেখ্য কঠিন হইয়া বলিল—ইংরাজিতে ‘বিজি-বডি’ বলে একটা শব্দ আছে, মানুষের দুর্ভাগ্য এই যে, সংসারে সর্বত্রই এই লোকগুলোর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। না হলে পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষার জন্য এমন ছুটোছুটি করে বাবাকেও আসতে হ’ত না, আমাকেও না। দেখুন অমরনাথবাবু, অনাহুত অপরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে আমি লজ্জাবোধ করি, কিন্তু অপরের যদি এ লজ্জাবোধ না থাকে ত অপ্রিয় হলেও কর্তব্য আমাকে করতেই হবে।
কন্যার কথা শুনিয়া সাহেবের ক্ষোভের সীমা রহিল না। হৃদয়ে যথার্থ বেদনা বোধ করিয়া কহিলেন—কাজের চেয়ে তোমাদের বাক্যগুলো যে ঢের বেশী কটু হচ্ছে, মা! বিশেষ করে যখন অমরনাথ আমাদের বাড়িতে এসেছেন।
মেয়ে কহিল—অমরনাথবাবু সম্ভ্রান্ত লোক, তথাপি বলার যদি কিছু আমার থাকে ত আমার নিজের বাড়ি ছাড়া আর কোথায় বলতে পারি বাবা? এ অপরাধ নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমা করবেন। আর অপরাধ যদি হয়েই থাকে, তাকে সম্পূর্ণ করে দেওয়াই ভাল।
আমাদের শিক্ষা-সংস্কার, আমাদের সংসার-যাত্রার বিধি-ব্যবস্থা অমরনাথবাবুর ধারণার সঙ্গে এক নয় বলেই যে আমাদের প্রজাদেরই আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলতে হবে, এ আমি কোনমতেই সঙ্গত মনে করিনে।
অমরনাথ উত্তর দিল—কাজ যদি আমাকে করতেই হয়, নিজের ধারণা নিয়েই করতে পারি। নইলে আপনার ধারণা অনুমান করে বেড়াবার মত সময় বা কল্পনা আমার নেই। একে যদি উত্তেজিত করা মনে করেন, উত্তেজিত করা ছাড়া আমার উপায় কি আছে?
আলেখ্য কহিল—তা হলে আত্মরক্ষা করা ছাড়া আমারই বা কি উপায় আছে, আপনি বলে দিতে পারেন?
রে-সাহেব দুই হাত উঁচু করিয়া ধরিয়া বাধা দিয়া বলিলেন—না, অমরনাথ, তুমি কিছুতেই এর জবাব দিতে পারবে না, এ আমি কোনমতেই হতে দিতে পারব না। এই বলিয়া একপ্রকার জোর করিয়া তাহাকে ঘরের বাহিরে লইয়া গেলেন। সিঁড়ির কাছে আসিয়া বলিলেন—অমরনাথ, আজ আমার বিস্ময়ের অবধি নেই।
অমরনাথ এ কথার তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিল—কেন?
রে-সাহেব বলিলেন—কেবল বিস্ময় নয়, বাবা, আমার দুঃখেরও আজ সীমা নেই।
বারান্দার একধারে ঘষা-কাচের একটা লন্ঠন ঝুলিতেছিল, সেই অস্পষ্ট আলোকে অমরনাথ বক্তার মুখের ‘পরে অকৃত্রিম বেদনার ছায়া দেখিতে পাইয়া বলিল—দুঃখ কিজন্যে রায়-মশায়? ওঁদের শিক্ষা ও সংস্কার যে আমাদের ধারণার সঙ্গে কিছুতেই মিলতে পারে না, এই ত স্বাভাবিক। তবে, আমার হয়ত এত কথা না বলাই শোভন ছিল, কিন্তু আপনার সমস্ত জমিদারির তিনিই না কি সত্যকার কর্ত্রী, তাই বোধ হয়, চুপ করে থাকতে পারলাম না। আপনার কাছে প্রগল্ভতা-প্রকাশের জন্য আমি লজ্জা বোধ করি, কিন্তু আপনি নিজে যদি আমাকে ক্ষমা করতে পারেন ত আমার তরফ থেকে দুঃখ করবার আর কিছুই নেই।
সাহেব বলিলেন—ক্ষমার কথাই বলো না অমরনাথ,—তোমাকে আমি যতটুকু জানতে পেরেছি, তাতে আমার কাছে তোমার অপরাধ বলে কিছু হতেই পারে না। দোষ অপরাধ নয় বাবা, আজ তোমাদের মস্ত বড় ভুল হয়ে গেল।
ভুল কিসের?
সাহেব বলিলেন—ভুল এই যে, তুমি যা বলেছো, সে-ও তোমার সত্য বলা নয়, এবং আলেখ্য যা-কিছু বলেছে, সমস্তই তার অপরের। সে জবাব তোমার কথার নয়।
সাহেবের কথা অমরনাথ বুঝিতে পারিল না, বুঝিবার জন্য পুনরায় জিজ্ঞাসা করিবার তাহার ইচ্ছাও ছিল না, সময়ও ছিল না। যাইবার জন্য নমস্কার করিয়া শুধু কহিল—কাজ আমার ঢের শক্ত হয়ে গেল, কিন্তু উপায় কি! প্রথম জীবনে যে ব্রত গ্রহণ করেছি, সারা জীবন ধরে তার উদ্যাপন আমাকে করতেই হবে।—এই বলিয়া সে অন্ধকার প্রাঙ্গণে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।
সাহেব ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিতেই আলেখ্য কহিল—বাবা, তুমি যতদিন বেঁচে আছ, জমিদারির সত্যিকার মালিক তুমি, আমি নয়। কোনদিন আমার হবে কি না, সে-ও ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু, আমাকে দিয়ে যদি বাস্তবিক শাসন করিয়ে নিতে চাও, আমি আমার বুদ্ধি-বিদ্যের মতই করতে পারি। কিন্তু, একবার এ-দিক, একবার ও-দিক যদি হয় ত, বরঞ্চ যা ছিল তাই থাক্, আগে যেরকম চলে আসছিল, তেমনই চলতে থাকুক!
তাহার পিতা জবাব দিলেন না, চুপ করিয়া আসিয়া তাঁহার চৌকিতে বসিলেন। এই নীরবতার তাৎপর্য আর কেহ বুঝিল না, বুঝিল শুধু আলেখ্য, কিন্তু বুঝিয়াও সে আপনাকে দমন করিতে পারিল না, কহিল—বাবা, তোমার কথায়, তোমার আচরণে অনেকে যারপরনাই প্রশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে। এ তুমি বুঝতে না পারো, কিন্তু আমি একেবারে হাড়ে হাড়ে বুঝছি।
সাহেব এ অভিযোগেরও কোন উত্তর দিলেন না, তেমনই মৌন হইয়াই বসিয়া রহিলেন। আগন্তুক অতিথিদ্বয়ও নীরবে রহিলেন; কারণ, এখন বোধ হয়, কন্যা ও পিতার মাঝখানে সহসা একটা কথা যোগ করিয়া আতিথ্যের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে তাঁহাদের বাধিল, কিন্তু তাঁহাদেরই মুখের ওপরে নিঃশব্দে অনুমোদনের সুস্পষ্ট আভাস দেখিতে পাইয়া আলেখ্যের উত্তেজনা চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল, কহিল—দেশে কি যে একটা হাওয়া এসেছে বাবা, কতকগুলি ভদ্রসন্তান হঠাৎ সমস্ত কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে একেবারে নিঃস্বার্থ পরোপকারে লেগে গেছেন, নিজেরা বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীস্ট হয়ে গেছেন, স্থির করেছেন, এক গালে চড় খেলে আর এক গাল পেতে দেবেন। গাল তাদের এবং সে সহিষ্ণুতা থাকে, পেতে দিন, আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই, কিন্তু সেই জোরে ত এ জোর প্রতিপন্ন হয় না বাবা যে, অপরের সম্পত্তি নিয়ে তারা যা খুশি তাই করতে পারেন। কেমন করে যেন তাদের বিশ্বাস হয়ে গেছে যে, যাদের কিছু আছে, তাদের ক্ষতি করতে পারলেই যাদের কিছু নেই তাদের পরম উপকার হয়ে যায়।
কমলকিরণ বোধ করি আর থাকিতে পারিলেন না, কহিলেন—এই যেমন বাবার গাড়ির উইন্ডস্ক্রীন ভেঙ্গে দেওয়া।
আলেখ্য কহিল—হ্যাঁ, কিন্তু এগুলো সহ্য করে যাওয়াই বোধ হয় কর্তব্য নয়।
কমলকিরণ কহিলেন—বাবারও ঠিক তাই মত।
উৎসাহ পাইয়া আলেখ্যের কণ্ঠস্বর অধিকতর তীব্র হইয়া উঠিল। কহিল—কিন্তু বিপদ হয়েছে এই যে, বাবার সে মত নয়। কিন্তু তুমি ত জান বাবা, এতকাল জমিদারির তুমি কোন খবর রাখনি। সমস্ত সিস্টেমটা একেবারে মরচে ধরে গেছে। সেইসব পরিষ্কার করতে গিয়ে যদি কেউ আত্মহত্যা করে বসে, সে কি আমার অপরাধ? কিন্তু সমস্ত আমার ঘাড়ে তুলে দিয়ে যারা হৈহৈ ক’রে বেড়াচ্ছে, আমি কোথাও মুখ দেখাতে পারিনে—না বাবা, হয় তুমি সত্যিই আমাকে ভার দাও, না হয়, যা ছিল তাই থাক, আমরা যেখান থেকে এসেছি সেখানে আবার ফিরে যাই।
এ অভিযোগ যে কাহার উপর, তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। সাহেব বিস্মিত হইয়া মুখ তুলিলেন এবং ক্ষুণ্ণস্বরে কহিলেন—কিন্তু অমরনাথ ত এ প্রকৃতির লোক নয় আলো! বরঞ্চ, আমি যেন তার কথার ভাবে বুঝলাম—
তাঁহার কথাটা শেষ হইল না, কমলকিরণ বলিয়া উঠিলেন—রাদার আমার মনে হয় মিস্টার রে, তিনিই জ্যাস্ট্ দি ম্যান্—এইসব পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত ভট্চায্যি বামুনগুলো—তোমার কি মনে হয় ইন্দু? ঠিক না—এই বলিয়া তিনি আলেখ্যের মুখের প্রতি চাহিয়া তাঁহার অসমাপ্ত বাক্য এইভাবেই শেষ করিলেন।
উত্তর-প্রত্যুত্তরের যে প্রবাহটা এতক্ষণ অনর্গল বহিয়া আসিতেছিল এইখানে তাহাতে বাধা পড়িল। কমলকিরণের বাক্য ও ইঙ্গিতের সমতা রক্ষা করিয়া আলেখ্যের মুখ দিয়া যাহা বাহির হইবে বলিয়া সকলে প্রত্যাশা করিল, তাহা বাহির হইল না। কারণ, অমরনাথ লোকটিকে পল্লীগ্রামের ব্রাহ্মণ বলিয়া গালাগালি দেওয়াও যদি বা চলে, অশিক্ষিত বলা চলে না। অন্ততঃ, শিক্ষার যে-সকল ট্রেডমার্ক, ছাপছোপ ভদ্রসমাজে প্রচলিত, তাহার অনেকগুলিই যে ওই লোকটির গায়ে ছাপ দেওয়া আছে, আলেখ্য তাহা জানিত। আরও একটা কথা এই যে, গাঙ্গুলী-মহাশয়ের আত্মহত্যায় বিচলিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া গ্রামের আর যাহারাই কেননা আন্দোলন করিয়া থাকুক, অমরনাথ করে নাই।
এ কথা শুধু সে তাহার নিজের মুখ হইতে নয়, অপরের মুখ হইতেও শুনিয়াছিল। স্বর্গীয় গাঙ্গুলীর দুর্ভাগ্য ও দুঃস্থ পরিবারের জন্য অমরনাথ অনেক করিয়াছে, কিন্তু আলেখ্যের বিরুদ্ধে বিষ ছড়াইবার প্রতিকূলেও সে কম যত্ন করে নাই। এ কথা সত্য, এবং সত্য বলিয়া আলেখ্যের নিজেরও বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, কিন্তু এখন ঝোঁকের উপর কথাটা যখন আর একপ্রকার দাঁড়াইল, বিরক্তির মাত্রাধিক্যে এই অনুপস্থিত লোকটির স্কন্ধে অপরাধের বোঝা চাপাইবার অশোভন উদ্যমে একটা মিথ্যা ভারও যখন চাপিয়া গেল, তখন তাহাকে মিথ্যা জানিয়াও আলেখ্য প্রতিবাদ করিতে পারিল না।
স্পষ্টই বুঝা গেল, সাহেব অন্তরে বেদনা বোধ করিলেন, কিন্তু শক্ত কথা সহজে তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইত না, মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে শুধু কহিলেন—তাই ত, এ কাজটা তার ভাল হয়নি। কিন্তু সাধারণতঃ এ রকম সে করে না।
কমলকিরণ কহিলেন—সাধারণতঃ, বাবার মোটরের কাচও লোকে ভাঙে না মিস্টার রে।
সাহেব বলিলেন—হুঁ।
কমলকিরণ কহিলেন—আমার মনে হয়, আলেখ্য যা বলছিলেন, এদের পরের উপকার, অর্থাৎ অপরের অপকার করার এ্যাক্টিভিটি একটু সংযত করে আনা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। কোন একটা এফেক্টিভ চেক—
সাহেব অন্যমনস্কভাবে বলিলেন—হুঁ, প্রয়োজন হলে করতেই হবে বৈ কি।
কমলকিরণ বলিলেন—আমাকে ক্ষমা করবেন মিস্টার রে, কিন্তু আপনি নিজে জমিদার হলেও অনেক বিষয়ে ইনডিফারেন্ট; আমি কয়েকটা বড় এস্টেটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে একটা ব্যাপার সর্বত্রই ওয়াচ্ করে যাচ্ছি! কতকগুলো স্বদেশী ছাপমারা প্যাট্রিয়টের পেশাই হয়ে দাঁড়িয়েছে জমিদার ও প্রজার মধ্যে বিরোধ বাধিয়ে দেওয়া। বলশেভিক প্রোপাগান্ডা ও তাদের টাকাই হচ্ছে এর মূলে। আপনি নিশ্চয় জানবেন মিস্টার রে, গভর্নমেন্ট এমন অনেক কথাই জানে, যা এদেশের জমিদাররা ড্রিমও করে না। গোড়াতেই বিশেষ একটু সচেতন না হলে সম্পত্তি হাতছাড়া হয়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়, আপনি নিশ্চয় জানবেন।—এই বলিয়া দুশ্চিন্তায় মুখ কালো করিয়া তিনি অপর দুইটি শ্রোতার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।
কিন্তু জমিদারি যাঁহার, তাঁহার মুখে আশঙ্কার কোন চিহ্ন প্রকাশ পাইল না, শান্তভাবে তিনি বলিলেন—পশ্চিমের ব্যাপার আমি ঠিক জানিনে বটে, কিন্তু আমাদের এই বাঙলাদেশে রাজা-প্রজার সম্বন্ধ একটু অন্য রকমের, কমল! কিছু করা যদি তোমরা দরকার বোঝ, কর, আমার আপত্তি নেই, কিন্তু ভয় পাবার কিছু নেই।
কমল প্রতিবাদ করিয়া প্রশ্ন করিলেন—পঁচিশ বৎসর পূর্বে যা ছিল, আজও ঠিক তাই আছে, কোন চেঞ্জ হয়নি, এ আপনি কি করে মনে করছেন?
সাহেব কহিলেন—চেঞ্জ হয়নি, এ ত আমি বলিনি।
কমল কহিলেন, আমিও ত ঠিক সেই ভয়ের কথাই বলছি মিস্টার রে।
সাহেব হাসিলেন। বলিলেন—কমল, শিক্ষার গুণে হোক, সময়ের গুণে হোক, জমিদারদের অত্যাচারের ফলে হোক, দেশের প্রজাদের মধ্যে যদি এতবড় পরিবর্তনই এসে থাকে, জমিদার তারা চায় না, দু-দিন আগে হোক, পরে হোক, তাদের যেতেই হবে, তোমরা কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। কিন্তু শুধু যদি আমার এই ছোট্ট জমিদারিটুকুর কথাই বল, তাহলে এই কথাটা আমার শুনে রাখ যে, প্রজাদের আমি বাস্তবিক ভালবাসি। জমিদার হিসাবে নিজে কখনও অত্যাচার করিনি, কর্মচারীদের সাধ্যমত করতে দিইনি। এ তারা জানে। আলো এই সম্বন্ধটুকুই যদি ভবিষ্যতে বজায় রেখে যেতে পারে ত তার ভয় নেই। কিন্তু আমার যে আবার রাত হয়ে যাচ্ছে—
এতক্ষণে বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে আলেখ্য একটি কথাও যোগ করে নাই, কিন্তু পিতা উঠিবার উপক্রম করিতেই সে বলিয়া উঠিল—বাবা, তুমি কি আমাকে লক্ষ্য করে এ কথা বললে?
পিতা সহাস্যে কহিলেন—লক্ষ্য করে কেন মা, তোমার নাম ধরেই ত এ কথা বললাম।
কন্যা জিজ্ঞাসা করিল—কতবার আমাদের প্রাপ্য খাজনা তুমি মাপ করে দিয়েছ, বাবা, একি তোমার মনে আছে?
আছে বৈ কি মা।
তুমি কি আমাকে প্রজাদের সেই অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে বল বাবা?
সাহেব সস্নেহকণ্ঠে ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—প্রাপ্য মানেই ন্যায্য নয় আলো—আমাদের যা প্রাপ্য, প্রজাদের তা ন্যায্য দেয় না-ও হতে পারে। আমি সেইটুকুই কেবল তাদের ক্ষমা করে এসেছি।
কমলকিরণ ইহার তাৎপর্য গ্রহণ করিতে পারিল না, কিন্তু আলেখ্য পারিল। ছেলেবেলা হইতেই পিতাকে সে অত্যন্ত ভালবাসিত।
মা তাঁহাকে দুর্বল বলিয়া যতই অবজ্ঞা করিতেন, ততই সে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিবার পথ খুঁজিয়া ফিরিত। ঘরের ও বাহিরের উৎপীড়ন ও অপমান হইতে তাঁহাকে অহরহ রক্ষা করিবার একান্ত চেষ্টায় এই শক্তিহীন মানুষটিকে একদিন সে সত্য সত্যই চিনিতে পারিয়াছিল! তাঁহার চিন্তা ও বাক্যের কোন অর্থ বুঝিতেই তাহার কোনদিন বিলম্ব ঘটিত না। আজিও বুঝিয়াও প্রশ্ন করিল—বাবা, এই কি তোমার আদেশ? এমনিভাবেই কি চলতে আমাকে তুমি উপদেশ দাও?
সাহেব তৎক্ষণাৎ বারংবার মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন—না মা, এ আমার আদেশ নয়, তোমার পিতার উপদেশও নয়। এ সংসারে সবাই একভাবে চলতে পারে না—শক্তির অভাবেও বটে, প্রবৃত্তির অভাবেও বটে। যদি পারো, মনে মনে খুশী হব, এইটুকুই শুধু তোমাকে বলতে পারি।
আলেখ্য কহিল—বাবা, আমার ভারী ইচ্ছে, কোথায় কি আছে, সব দেখে আসি। যেখানে হাঙ্গামা বেধেছে, নিজে একবার সেখানে যাই।
সাহেব সম্মতি দিয়া কহিলেন—বেশ ত মা, কালই আমি ম্যানেজারবাবুকে ডেকে সমস্ত উদ্যোগ করে দিতে বলবো। নদীতে এখন জল আছে, হয়ত শেষ পর্যন্তই বজরা যেতে পারবে।
ইন্দু এতক্ষণ কোন কথা কহে নাই, জল-যাত্রার প্রস্তাবে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, বলিল—আমিও তোমার সঙ্গে যাবো, আলো। কমলের প্রতি চাহিয়া কহিল, দাদা, তোমার কি এ সময়ে খুব জরুরী কাজ আছে? দু-চারদিন থেকে যেতে পারবে না?
কেন বল ত?
ইন্দু বলিল—আমাদের সঙ্গে যেতে। ছোট্ট নদী দিয়ে নৌকোর মধ্যে যাওয়া-আসা, এ ত তোমার কক্ষণো হয়নি দাদা। যাবে?
কমলকিরণ আলেখ্যের মুখের ভাব লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে তখন অন্যত্র চাহিয়াছিল। মুখ দেখা গেল না, কিন্তু ভগিনীর আবেদনের ইঙ্গিত উপলব্ধি করিল। বুকের মধ্যে তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রাণপণে তাহা সংবরণ করিয়া নিস্পৃহকন্ঠে কহিল—দেরি হয়ে যেতে পারে, কিন্তু—আচ্ছা বেশ, না হয় যাবো।
সাহেব ধীরে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন— সেই ভাল। কিন্তু অমরনাথও শুনলাম যাবে; দেখো, যেন একটা বিবাদ না হয়। কিন্তু আমি এখন উঠি ইন্দু, গুড্নাইট। এই বলিয়া চিন্তান্বিত মুখে আস্তে আস্তে তিনি ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন।
জাগরণ – ০৮
আট
এই রায়-পরিবারের জমিদারিটি আয়তনে ছোট, কিন্তু তাহার মুনাফা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ছিল না। জমিদার চিরদিন প্রবাসে থাকেন, সুতরাং সমস্তই কর্মচারীদের হাতে; এ অবস্থায় কাজকর্ম নিতান্ত বিশৃঙ্খল হইবার কথা, কিন্তু প্রজারা ধর্মভীরু বলিয়াই হউক, বা অন্যমনস্ক-প্রকৃতি উদাসীন রে-সাহেবের ভাগ্যফলেই হউক, মোটের উপর ভালভাবেই এতদিন ইহা পরিচালিত হইয়া আসিয়াছিল। কেবল উত্তরোত্তর আয় বাড়ানোর কাজটাই এতকাল স্থগিত ছিল বটে, কিন্তু চুরিটাও তেমনি বন্ধ ছিল। আলেখ্যের হাতে আসিয়া এই স্বল্পকালের মধ্যেই ইহার চেহারায় একটা পরিবর্তন দেখা দিয়াছে। সুশৃঙ্খলিত করিবার অভিনব উদ্যম এখনও প্রজাদের গৃহ পর্যন্ত অতদূরে পৌঁছায় নাই বটে, কিন্তু তাহার আকর্ষণের কঠোরতা কর্মচারিবর্গ অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বৃদ্ধ নয়ন গাঙ্গুলীর আত্মহত্যার পরে হঠাৎ মনে হইয়াছিল বটে, হয়ত ইহা এইখানেই থামিবে, কিন্তু হাটের ব্যাপার লইয়া আলেখ্যের কর্মশীলতা পুনরায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। যে আকস্মিক দুর্ঘটনা এই কয়দিন তাহাকে লজ্জিত বিষণ্ণ করিয়া রাখিয়াছিল, কাল অমরনাথের সহিত মুখোমুখি একটা বচসার মত হইয়া যাইবার পরে সে ভাবটাও আজ তাহার কাটিয়া গিয়াছিল। তাহার মনের মধ্যে আর সন্দেহমাত্র ছিল না যে, এ সংসারে যাহাদের কোথাও কিছু আছে, তাহা কোনক্রমে নষ্ট করিয়া দেওয়াটাকেই কতকগুলি লোক দেশের সবচেয়ে বড় কাজ বলিয়া ভাবিতে শুরু করিয়া দিয়াছে এবং অমরনাথ যত বড় অধ্যাপকই হউক, সে-ও এই দলভুক্ত।
স্থির হইয়াছিল, সম্পত্তির কোথায় কি আছে, নিজে একবার পরিদর্শন করিয়া আসিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যেই আজ সকাল হইতে বৃদ্ধ ম্যানেজারবাবুকে সুমুখে রাখিয়া আলেখ্য কমলকিরণের সাহায্যে একটা ম্যাপ তৈরি করিতেছিল। পথঘাট ভাল করিয়া জানিয়া রাখা প্রয়োজন। উভয়ের উৎসাহের অবধি নাই, দিনের স্নানাহার আজ কোনমতে সারিয়া লইয়া পুনরায় তাঁহারা সেই কর্মেই নিযুক্ত হইলেন। এমনি করিয়া বেলা পড়িয়া আসিল।
সঙ্গীর অভাবে ইন্দু মাঝে মাঝে গিয়া তাহাদের টেব্লে বসিতেছিল, কিন্তু সেখানে তাহার প্রয়োজন নাই, তাই অধিকাংশ সময়ই বাটীর চারি পাশে একাকী ঘুরিয়া বেড়াইয়া সময় কাটাইবার চেষ্টা করিতেছিল। এমনি সময়ে দেখিতে পাইল, সাহেব পদব্রজে বাহির হইয়া যাইতেছেন। দ্রুতপদে তাঁহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইতে সাহেব চকিত হইয়া কহিলেন—তুমি একলা যে ইন্দু?
ইন্দু কহিল—দাদারা ম্যাপ তৈরি করছেন, এখনও শেষ হয়নি।
কিসের ম্যাপ?
ইন্দু কহিল—তাঁরা জমিদারি দেখতে যাবেন, পথ-ঘাট কোথায় আছে না আছে, সেই সমস্ত ঠিক করে নিচ্ছেন।
সাহেব সহাস্যে বলিলেন—আর সেখানে তোমার কোন কাজ নেই, না ইন্দু?
ইন্দু হাসিয়া সে কথা চাপা দিয়া কহিল—আপনি কোথায় যাচ্ছেন, কাকাবাবু?
এই সম্বোধন আজ নূতন। সাহেব পুলকিত বিস্ময়ে ক্ষণকাল তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিলেন—আমার ছেলেবেলার এক সঙ্গী পীড়িত হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছেন, তাঁকেই একবার দেখতে যাচ্ছি, মা।
—আপনার সঙ্গে যাব কাকাবাবু?
সাহেব কহিলেন, সে যে প্রায় মাইল-খানেক দূরে, ইন্দু। তুমি ত অতদূরে হাঁটতে পারবে না, মা।
আমি আরও ঢের বেশী হাঁটতে পারি, কাকাবাবু।—এই বলিয়া সে সাহেবের হাত ধরিয়া নিজেই অগ্রসর হইয়া পড়িল। গাড়িখানা প্রস্তুত করিয়া সঙ্গে লইবার প্রস্তাব সাহেব একবার করিলেন বটে, কিন্তু ইন্দু তাহাতে কান দিল না।
গ্রাম্যপথ। সুনির্দিষ্ট চিহ্ন বিশেষ নাই। পুকুরের পাড় দিয়া, গোয়ালের ধার দিয়া, কোথাও বা কাহারও প্রাঙ্গণের ভিতর দিয়া গিয়াছে, ইন্দু সঙ্কোচ বোধ করিতে লাগিল। ছেলেমেয়েরা ছুটিয়া আসিল, পুরুষরা জমিদার দেখিয়া কাজ ফেলিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইতে লাগিল, বধূরা দূর হইতে অবগুণ্ঠনের ফাঁক দিয়া কৌতূহল মিটাইতে লাগিল। একটুখানি নিরালায় আসিয়া ইন্দু কহিল, এরা আমাদের মত মেয়েদের বোধ হয় আর কখনও দেখেনি, না?
সাহেব ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন—খুব সম্ভব তাই।
ইন্দু কহিল, এদের চোখে আমরা যেন কি এক রকম অদ্ভুত হয়ে গেছি, না কাকাবাবু? —কথাটি বলিতে হঠাৎ যেন তাহার একটুখানি লজ্জা করিয়া উঠিল।
সাহেব জবাব দিলেন না, শুধু একটু হাসিলেন। দুই-চারি পা নিঃশব্দে চলিয়া ইন্দু বলিয়া উঠিল—এরা কিন্তু এক হিসেবে বেশ আছে, না কাকাবাবু?
সাহেব পুনরায় হাসিলেন, কহিলেন—এক হিসেবে সংসারে সবাই ত বেশ থাকে, মা।
ইন্দু বলিল—সে নয়, কাকাবাবু। এক হিসেবে আমাদের চেয়ে এরা ভাল আছে, আমি সেই কথাই বলছি।
বৃদ্ধ ইহার কোন স্পষ্ট উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আচ্ছা মা, এদের মত কি তোমরাও এমনিভাবে জীবন যাপন করতে পার?
ইন্দু কহিল—তোমরা আপনি কাদের বলছেন, আমি জানিনে। যদি আলোকে বলে থাকেন ত সে পারে না। যদি আমাকে বলে থাকেন ত আমি বোধ করি পারি।—এই বলিয়া সে মুহূর্তকাল, মৌন থাকিয়া আস্তে আস্তে বলিতে লাগিল—বাবা-মা আমার ওপরে বেশী খুশী নন, আমাদের সমাজের মেয়েরা লুকিয়ে আমাকে ঠাট্টা-তামাশা করে, কিন্তু কি জানি কাকাবাবু, আমার ভেতরে কি আছে, আমি কিছুতেই তাদের সঙ্গে সমানভাবে মিশতে পারিনে। অনেক সময়েই আমার যেন মনে হয়, যেভাবে আমরা সবাই থাকি, তার বেশীর ভাগই সংসারে নিরর্থক। মা বলেন, সভ্যতার এ-সকল অঙ্গ, সভ্য মানুষের এ-সব অপরিহার্য। কিন্তু আমি বলি, ভালই যখন আমার লাগে না, তখন অত সভ্যতাতেই বা আমার দরকার কিসের?
তাহার কথা শুনিয়া, তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া সাহেব মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন, কিছুই বলিলেন না। ইন্দু অযাচিত অনেক কথা বলিয়া ফেলিয়া নিজের প্রগল্ভতায় লজ্জা পাইল। তাহার চৈতন্য হইল যে, সাহেবের মুখের উপর আধুনিক সভ্যতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে যাওয়া ঠিক হয় নাই। এখন কতকটা সামলাইয়া লইবার অভিপ্রায়ে কহিল, যাঁদের এ-সব ভাল লাগে, তাঁদের সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিনি, কাকাবাবু। কিন্তু যাঁদের ভাল লাগে না, বরঞ্চ কষ্ট বোধ হয়, তাঁদের এততে দরকার কি? আপনি কিন্তু আমার ওপর রাগ করতে পারবেন না, তা বলে দিচ্ছি।
সাহেব প্রত্যুত্তরে শুধু হাসিমুখে কহিলেন,—না মা, রাগ করিনি।
ইন্দু বলিতে লাগিল—এই যে-সব মেয়েরা সসঙ্কোচে পথের একধারে সরে দাঁড়াচ্ছে, পুরুষরা সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে কেউ আপনাকে প্রণাম করছে, কেউ সেলাম করছে, এদের সঙ্গে আমাদের কিছুই ত মেলে না, কিন্তু এরা কি সব বর্বর? হ’লই বা খালি গা, খালি পা, তাতে লজ্জা কিসের? পরকে সম্মান দিতে ত এরা আমাদের চেয়ে কম জানে না, কাকাবাবু?
বৃদ্ধ এ প্রশ্নেরও কোন জবাব দিলেন না, তেমনি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।
ইন্দু কহিল—আপনি একটা কথারও আমার জবাব দিলেন না, মনে মনে বোধ হয় বিরক্ত হয়েছেন।
এবার বৃদ্ধ কথা কহিলেন; বলিলেন—এটি কিন্তু তোমার আসল কথা নয়, মা। তুমি ঠিক জানো, তোমার বুড়ো কাকাবাবু মনে মনে তোমাকে আশীর্বাদ করছেন বলেই কথা কবার তাঁর ফুরসত হচ্ছে না। আচ্ছা, তোমার দাদা কি বলেন, ইন্দু?—এই বলিয়া তিনি উৎসুকনেত্রে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। এই ঔৎসুক্যের হেতু বুঝিতে ইন্দুর বিলম্ব হইল না, কিন্তু ইহার ঠিক কি উত্তর যে সে দিবে, তাহাও ভাবিয়া পাইল না।
কোন-কিছুর জন্যই নিরতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করা বৃদ্ধের স্বভাব নয়, ইন্দুর এই অবস্থা-সঙ্কট অনুভব করিয়া তিনি অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাদের কবে যাবার দিন স্থির হল মা?
কোথায় কাকাবাবু?
জমিদারি দেখতে।
ইন্দু কহিল—আমাকে তাঁরা এখনও জানান নি। কিন্তু যদি সম্ভব হয়, সে-ক’টা দিন আমি আপনাদের কাছে থাকতে পারলেই ঢের বেশী খুশী হব, কাকাবাবু।
বৃদ্ধ কহিলেন—মা, এই আমার বন্ধুর বাড়ি। এস, ভেতরে চল।
ইন্দু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—ঐ ত সুমুখে খোলা মাঠ দেখা যাচ্ছে, কাকাবাবু, আমি কেন আধঘণ্টা বেড়িয়ে আসি না? আমার সঙ্গে ত এদের কোনরূপ পরিচয় নেই।
বৃদ্ধ কহিলেন—ইন্দু, এ আমাদের পাড়াগাঁ, এখানে পরিচয়ের অভাবে কারও ঘরে যাওয়ায় বাধে না। কিন্তু তোমাকে আমি জোর করতেও চাইনে।—একটু হাসিয়া বলিলেন, তবে রোগীর ঘরের চেয়ে খোলা মাঠ যে ভাল, এ আমি অস্বীকার করিনে। যাও, শুধু এইটুকু দেখো, যেন পথ হারিয়ো না।—এই বলিয়া তিনি ইন্দু অগ্রসর হইতেই কহিলেন, আর এই মাঠের পরেই বরাট গ্রাম। যদি খানিকটা এগোতে পারো, সুমুখেই অমরনাথের টোল দেখতে পাবে। যদি দেখা হয়েই যায় ত বলো, কাল যেন সে আমার সঙ্গে একবার দেখা করে। এই বলিয়া তিনি সদরের দ্বার ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।
জাগরণ – ০৯
নয়
মাঠের ধার দিয়া চলন-পথ বরাবর বরাট গ্রামে গিয়ে পৌঁছিয়াছে, কাহাকেও জিজ্ঞাসা না করিয়াও ইন্দু সোজা গিয়া গ্রামের তেমাথায় উপস্থিত হইল। বিরাট একটা বটবৃক্ষের ছায়ায় অমরনাথের চতুষ্পাঠী, দশ-বারোজন ছাত্রপরিবৃত হইয়া তিনি ন্যায়ের অধ্যাপনায় নিযুক্ত, এমনি সময় ইন্দু গিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল। অতি বিস্ময়ে প্রথমে অমরনাথের বাক্যস্ফূর্তি হইল না, কিন্তু পরক্ষণে সশিষ্য গাত্রোত্থান করিয়া বহুমানে সংবর্ধনা করিয়া কহিলেন—একি আমার পরম ভাগ্য! আর সকলে কোথায়?
একজন ছাত্র আসন আনিয়া দিল। অনভ্যাসবশতঃ ইন্দুর প্রথমে মনে পড়ে নাই, সে আর একবার নীচে নামিয়া গিয়া, জুতা খুলিয়া রাখিয়া আসনে আসিয়া উপবেশন করিয়া কহিল—আমি একাই এসেছি, আমার সঙ্গে কেউ নেই।
কথাটা বোধ হয় অমরনাথ ঠিক প্রত্যয় করিতে পারিলেন না, স্মিতমুখে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন।
ইন্দু কহিল—কাকাবাবুর সঙ্গে আমি বেড়াতে বার হয়েছিলাম। তিনি তাঁর এক পীড়িত বন্ধুকে দেখতে গেলেন। আমাকে বললেন, আপনাকে খবর দিতে, যদি পারেন, কাল একবার দেখা করবেন।
অমরনাথ কহিলেন—খবর দেবার জন্য ত জমিদারের লোকের অভাব নেই। কিন্তু এই যদি যথার্থ হয় ত বলতেই হবে এ আমার কোন্ অজানা পুণ্যের ফল। কিন্তু কার বাড়িতে রায়-মশায় এসেছেন শুনি?
ইন্দু কহিল—আমি ত তাঁর নাম জানিনে, শুধু বাড়িটা চিনি। কিন্তু আপনার নিজের বাড়ি এখান থেকে কতদূরে অমরনাথবাবু?
অমরনাথ কহিলেন—মিনিট দুয়ের পথ।
—আমাকে তা হলে একটু খাবার জল আনিয়ে দিন।
একজন ছাত্র ছুটিয়া চলিয়া গেল এবং ক্ষণকাল পরেই সাদা পাথরের রেকাবিতে করিয়া খানিকটা ছানা এবং গুড় এবং তেমনি শুভ্র পাথরের পাত্রে শীতল জল আনিয়া উপস্থিত করিল। প্রয়োজন নাই বলিয়া ইন্দু প্রত্যাখ্যান করিল না, ছানা ও গুড় নিঃশেষ করিয়া আহার করিল এবং জলপান করিয়া কহিল—এখন তা হলে আমি উঠি?
অমরনাথ এই শিক্ষিতা মেয়েটির নিরভিমান সরলতায় মনে মনে অত্যন্ত প্রীত হইয়া কহিলেন—অনাহূত আমার পাঠশালায় এসেই কিন্তু চলে যেতে আপনি পাবেন না। দরিদ্র ব্রাহ্মণের কুটীরেও একবার আপনাকে যেতে হবে। সেখানে আমার মা আছেন, দিদি আছেন, ছোটবোন শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছেন। তাঁদের দেখা না দিয়ে আপনি যাবেন কি করে? চলুন।
ইন্দু তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া কহিল—চলুন। কিন্তু সন্ধ্যা হতে ত দেরি নেই, কাকাবাবু যে ব্যস্ত হবেন?
অমরনাথ সহাস্যে কহিলেন—ব্যস্ত হবেন না। কারণ, তাঁকে খবর দিতে লোক গেছে।
টোল-ঘরের পিছন হইতেই বাগান শুরু হইয়াছে। একটা মস্ত বড় পুকুর, তাহার চারিধারে কত যে ফুলগাছ এবং কত যে ফুল ফুটিয়া আছে, তাহার সংখ্যা নাই। অমরনাথের পিছনে সদর-বাটীতে প্রবেশ করিয়া ইন্দু দেখিল, প্রশস্ত চণ্ডীমণ্ডপের একধারে দিনান্তের শেষ আলোকে বসিয়া জন-দুই ছাত্র তখনও পুঁথি লিখিতেছে, অন্যধারে পাঁচ-সাতটি চিক্কণ পরিপুষ্ট সবৎসা গাভী ভূরিভোজনে নিযুক্ত, একটা মস্ত বড় কালো কুকুর একমনে তাহাই নিরীক্ষণ করিতেছিল, অভ্যাগত দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ল্যাজ নাড়িয়া অভ্যর্থনা করিল। সমস্ত পূর্বদিকটা বড় বড় ধানের মরাই গৃহস্থের সৌভাগ্য সূচিত করিতেছে; একটা জবার গাছ ফুলে ফুলে একেবারে রাঙ্গা হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দু ভাল করিয়া সমস্ত পর্যবেক্ষণ করিয়া অন্দরে প্রবেশ করিল।
মাটির বাড়ি। আট-দশটি উচ্চ প্রশস্ত ঘর। প্রাঙ্গণ এমন করিয়াই নিকানো যে, জুতা পায়ে দিয়া প্রবেশ করিতে ইন্দুর যেন গায়ে লাগিল। সেইমাত্র সন্ধ্যা হইয়াছে, ধূপধুনা ও গুগ্গুলের গন্ধে সমস্ত গৃহ যেন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।
অমরনাথের বিধবা দিদি ঠাকুরঘরে ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু খবর পাইয়া তাহার মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ছোটবোন ছেলে কোলে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ইন্দু অমরনাথের জননীকে প্রণাম করিল। তিনি হাত দিয়া তাহার চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন এবং যে দুই-চারিটি কথা উচ্চারণ করিলেন, তাহাতে ইন্দুর মনে হইল, এত বড় আদর ইহজীবনে আর কখনও সে পায় নাই। দাওয়ার উপরে বসিতে তিনি স্বহস্তে আসন পাতিয়া দিলেন।
ইন্দু উপবেশন করিলে অমরের জননী কহিলেন—গরীবের ঘরে ঠিক সন্ধ্যার সময় আজ মা কমলা এলেন।
ইন্দু শিক্ষিতা মেয়ে, কিন্তু মুখে তাহার হঠাৎ কথা যোগাইল না। শিক্ষা, সংস্কার ও অভ্যাসবশতঃ জাতির কথা তাহাদের মনেও হয় না, কিন্তু আজ এই শুদ্ধাচারিণী বিধবা জননীর সম্মুখে কেমন যেন তাহার সঙ্কোচ বোধ হইল। কহিল—মা, আপনারা ব্রাহ্মণ, কিন্তু আমি কায়স্থের মেয়ে। আপনি আসন পেতে দিলেন?
গৃহিণী স্নিগ্ধহাস্যে কহিলেন—তুমি যে সন্ধ্যার সময়ে আমার ঘরে লক্ষ্মী এলে। দেবতার কি জাত থাকে, মা? তুমি সকল জাতের বড়।
অমরের ছোটবোন বোধ হয় ইন্দুর সমবয়সী। সে কাছে আসিয়া বসিতেই ইন্দু তাহার ছেলেকে কোলে টানিয়া লইল।
মা জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার নামটি কি মা?
ইন্দু কহিল—মা, আমার নাম ইন্দু।
মা কহিলেন—তাই ত বলি মা, নইলে কি কখনও এমন মুখের শ্রী হয়!
ইন্দু অত্যন্ত লজ্জা পাইয়া মুচকিয়া হাসিয়া কহিল—কিন্তু আর একদিন এলে যে তখন কি বলবেন, আমি তাই শুধু ভাবি।
মাও হাসিয়া কহিলেন—ভাবতে হবে না মা, আমিই ভেবে রেখেছি, সেদিন তোমাকে কি বলবো। কিন্তু আসতে হবে।
ইন্দু স্বীকার করিল। অমরের দিদি ঠাকুরঘর হইতে ছুটি পাইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন; কহিলেন—ঠাকুরের আরতি হতে বেশী দেরি নেই ইন্দু, তোমাকে কিছু-একটু মুখে দিয়ে যেতে হবে।
ইন্দু তাঁহার পরিচয় অনুমান করিয়া লইয়া বলিল, খাওয়া আমার আগেই হয়ে গেছে দিদি, আর একদিন এসে ঠাকুরের প্রসাদ পেয়ে যাবো, আজ আর আমার পেটে জায়গা নেই।—এই বলিয়া সে পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিল যে, এ স্থান ত্যাগ করিবার পূর্বে আর একদিন আসিয়া সে ঠাকুরের প্রসাদ ও মায়ের পায়ের ধূলা গ্রহণ করিয়া যাইবে।
ইন্দু বাটী হইতে যখন বাহির হইল, তখন সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকার গাঢ় হইয়া আসিতেছিল। অমরনাথের হাতে একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন। ইন্দু কহিল—আলোটা আর কাউকে দিন আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।
অমরনাথ কহিলেন—পৌঁছে দেবার লোক আমি ছাড়া আর কেউ নেই।
তার মানে?
তার মানে আপনি অনাহূত আমার ঘরে এসেছিলেন। এখন পৌঁছে দিতে যদি আর কেউ যায় ত আমার অধর্ম হবে।
কিন্তু ফিরতে যে আপনার রাত্রি হয়ে যাবে, অমরনাথবাবু?
তার আর উপায় কি? পাপ অর্জন করার চেয়ে সে বরঞ্চ ঢের ভাল।
ইন্দু কহিল—তবে চলুন। কিন্তু আজ আমার একটা ভুল ভেঙ্গে গেল। আমরা সবাই আপনাকে বড় দরিদ্র ভাবতাম।
অমরনাথ মৌন হইয়া রহিলেন।
ইন্দু কহিল—আপনাদের বাড়ি ছেড়ে আমার আসতে ইচ্ছে করছিল না। আমার ভারী সাধ হয় আলোদের বাড়ি ছেড়ে আমি দিন-কতক মায়ের কাছে এসে থাকি।
অমরনাথ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন—অত বড় সৌভাগ্যের কল্পনা করতেও আমাদের সাহস হয় না। (‘মাসিক বসুমতী’, বৈশাখ, ১৩৩২)
[—অসমাপ্ত]
দিন-কয়েকের ভ্রমণ-কাহিনী
নলিনী,- তোমার যাবার পরে আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে, দিন-কয়েক বাহিরে যাওয়ার অজুহাতে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লেখার বিপদ আছে। প্রথম, এই জাতীয় লেখা আমার আসে না; অনধিকারচর্চা অপরাধে আমার পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ জলধর ভায়া হয়ত রাগ করিবেন। লোকেও অপবাদ দিয়া বলিবে, এ শুধু তাঁহার নৈহাটী ও বরানগর ভ্রমণ-বৃত্তান্তের নিছক নকল। দ্বিতীয় বিপদ শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয়। কারণ, আমি যদি বলি, দিল্লীতে এবার রেলওয়ে স্টেশন দেখিয়া আসিলাম, তিনি হয়ত কাগজে প্রতিবাদ করিয়া বলিবেন, ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র উপন্যাস লিখিয়াছেন। দিল্লীতে স্টেশন বলিয়া কোন-কিছুই নাই, ওখানে রেলগাড়িই যায় না। অতএব, মুশকিল বুঝিতেই পারিতেছ। তবে, গোটাকয়েক নিজের মনের কথা বলা যাইতে পারে। চৌধুরী-মশায় উপন্যাস বলিলেও দুঃখ নাই, শ্রীমান্ রায়বাহাদুর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত নয় বলিলেও আপসোস হইবে না।
আমার যাওয়ার ইতিহাস এই প্রকার।
প্রায় মাসখানেক পূর্বে বন্ধুরা একদিন বলিলেন, দেশোদ্ধার করিতে অনেকে দিল্লী কংগ্রেসে যাইতেছেন, তুমিও চল। অস্বীকার করিয়া ফল নাই জানিয়া রাজী হইলাম। ভরসা ছিল, অন্যান্য বারের মত এবারেও ঠিক যাইবার দিন পেটের অসুখ করিবে। কিন্তু এবার তাঁহারা এরূপ দৃষ্টি রাখিলেন যে, তাহার সুযোগই ঘটিল না, রওনা হইতে হইল। সন্ধ্যা নাগাদ আমার প্রবাসের বাহন ভোলার স্কন্ধে আত্মসমর্পণ করিয়া মেল ট্রেনে চাপিয়া বসিলাম। ট্রেনের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। আফিমের ঘোরে সারারাত্রি ধরিয়া আমি তামাক খাইলাম, এবং আমার একমাএ অপরিচিত সহযাত্রী আমাশার বেগে আলো জ্বালাইয়া সারারাত্রি ধরিয়া পায়খানায় গেলেন। ভোর নাগাদ আমিও শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম, তাঁহারও হাত-পা অশক্ত অবশ হইয়া আসিল। সুতরাং আলো নিবাইয়া উভয়েই কিয়ৎকাল নিদ্রা দিলাম। সকালে কোন একটা স্টেশনে নামিবার সময় জলের সোরাইটা আমার তিনি দিলেন ভাঙ্গিয়া, এবং উহার টাইম-টেবল্টা আমি রাখিলাম বালিশের নীচে চাপিয়া। অতঃপর বাকী পথটা একাকী নিরুপদ্রবে কাটিল, অবিশ্রাম তামাক খাইয়া গাড়ির ফুলকাটা সাদা ছাতটা কালো করিয়া দিলাম।
এবার দিল্লী কংগ্রেসের পালা। এ সম্বন্ধে এত লোকে এত কলরব এত আস্ফালন করিয়াছে, এত গালি দিয়াছে, জ্বালা ও উদ্দাম আবর্তনের জন্মদান করিয়াছে যে, সেখানে অন্তর বস্তুটি আমার প্রবেশ করিবার বাস্তবিকই পথ খুঁজিয়া পায় নাই। কেবল সাধারণের পরিত্যক্ত, অতি সঙ্কীর্ণ নিরালা একটুখানি পথ সন্ধান করিয়া পাইয়াছিলাম, এবং সেইজন্যই শুধু আমার মনে হয়, মনের মধ্যেটা আমার নিছক ব্যর্থতার গ্লানিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে পারে নাই।
বাঙ্গালার দেশবন্ধু দাশকে অতিশয় কাছে করিয়া দেখিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। যতই দেখিয়াছি, ততই অকপটে মনে হইয়াছে, এই ভারতবর্ষের এত দেশ এত জাতির মানুষ দিয়া পরিপূর্ণ বিরাট বিপুল এই জনসঙেঘর মধ্যেও এতবড় মানুষ বোধ করি আর একটিও নাই। এমন একান্ত নির্ভীক, এমন শান্ত সমাহিত, দেশের কল্যাণে এমন করিয়া উৎসর্গ-করা জীবন আর কৈ? অনেকদিন পূর্বে তাঁহারই একজন ভক্ত আমাকে বলিয়াছিলেন, দেশবন্ধুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা এবং বাঙ্গালাদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা প্রায় তুল্য কথা। কথাটা যে কত বড় সত্য, এই সভার একান্তে বসিয়া আমার বহুবারই তাহা মনে পড়িয়াছে। অথচ, এই বাঙ্গালাদেশেরই কাগজে কাগজে যে তাঁহাকে ছোট বলিয়া লাঞ্ছিত করিয়া, পরের চক্ষে হীন করিয়া প্রতিপন্ন করিবার অবিশ্রাম চেষ্টা চলিয়াছে, এতবড় ক্ষোভের বিষয় কি আর আছে? তাঁহাকে ক্ষুদ্র করিয়া দাঁড় করানোর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বাঙ্গালাদেশটাই যে অপরের চক্ষে ক্ষুদ্র হইয়া আসিবে, এমন সহজ কথাটাও যাঁহারা অনুভব করিতে পারেন না, তাঁহাদের লেখার ভিতর দিয়া দেশের কোন্ শুভকার্য সম্পন্ন হইবে? একের সঙ্গে অপরের মত ষোল-আনা মিলিতে না পারে, হয়ত মিলেও না, কিন্তু মতামতের চাইতেও এই মানুষটি যে কত বড়, এ কথা লোকে এত সহজে ভুলিয়া যায় কি করিয়া? তাঁহার প্রতি চাহিয়া বিভিন্ন জনতার এই বিপুল হট্টগোলের মাঝখানে বসিয়াও এ কথা আমার বারবার মনে হইয়াছে যে, এই সাধারণ মানুষটি তাঁহার জীবদ্দশায় কতখানি দেশোদ্ধার করিয়া যাইবেন, তাহা ঠিক জানি না, কিন্তু যে অসাধারণ চরিত্রখানি তিনি দেশবাসীর অনাগত বংশধরগণের জন্য রাখিয়া যাইবেন, তাহা তার চেয়েও সহস্র গুণে বড়। কাগজের গালিগালাজ এই পরাধীন দেশকে কোনদিনই স্বাধীনতা দিবে না, যে দিবে, সে শুধু এই সকল চরিত্রের ইতিহাস।
এই জাতীয় কংগ্রেসের আর একটা ব্যাপার আমার বেশ মনে আছে, সে হিন্দু-মোসলেম ইউনিটি। এই ইউনিটির এক অধ্যায় ইতিপূর্বেই সাহারানপুরে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছিল। সভাপতি মৌলানা আজাদ সাহেব নাকি উর্দুতে দু-চার কথা বলিয়াছিলেন, কিন্তু মহাত্মাজীর অশেষ প্রীতিভাজন মৌলনা মহম্মদ আলি এ সম্বন্ধে নীরব হইয়া রহিলেন। তা থাকুন, কিন্তু তথাপি শুনিতে পাইলাম, হিন্দু-মোসলেম ইউনিটি একদিন জাতীয় মহাসভার মধ্যে সম্পন্ন হইয়া গেল। সবাই বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বলিতে লাগিল—যাক, বাঁচা গেল। চিন্তা আর নাই, নেতারা হিন্দু-মুসলমান সমস্যার শেষ-নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন, এবার শুধু কাজ আর কাজ,—শুধু দেশোদ্ধার। প্রতিনিধিরা ছুটি পাইয়া সহাস্যমুখে দলে দলে টাঙ্গা, এক্কা এবং মোটর ভাড়া করিয়া প্রাচীন কীর্তিস্তম্ভসকল দেখিতে ছুটিলেন।
সে ত আর এক-আধটা নয়, অনেক। সঙ্গে গাইড, হাতে কাগজ পেন্সিল—কোন্ কোন্ মস্জেদ কয়টা হিন্দু মন্দির ভাঙ্গিয়া তৈয়ার হইয়াছে, কোন্ ভগ্নস্তূপের কতখানি হিন্দু ও কতখানি মোসলেম, কোন্ বিগ্রহের কে কবে নাক এবং কান কাটিয়াছে ইত্যাদি বহু তথ্য ঘুরিয়া ঘুরিয়া সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। অবশেষে শ্রান্তদেহে দিনের শেষে গাছতলায় বসিয়া পড়িয়া অনেকেরই দীর্ঘশ্বাসের সহিত মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিতে শুনিলাম—উঃ! হিন্দু-মোসলেম ইউনিটি! (‘বিজলী’, ২৫ আশ্বিন ১৩৩০)
মানুষের অত্যন্ত সাধের বস্তুই অনেক সময়ে অনাদরে পড়িয়া থাকে। কেন যে থাকে জানি না, কিন্তু নিজের জীবনে বহুবার লক্ষ্য করিয়াছি, যাহাকে সবচেয়ে বেশী দেখিতে চাই, তাহার সঙ্গেই দেখা করা ঘটিয়া উঠে না, যাহাকে সংবাদ দেওয়া সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন, সেই-ই আমার চিঠির জবাব পায় না। শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ধামটিও ঠিক এমনি। সুদীর্ঘ জীবনে মনে মনে ইহার দর্শনলাভ কত যে কামনা করিয়াছি তাহার অবধি নাই, অথচ আমার পশ্চিমাঞ্চলে যাতায়াতের পথের কখনো দক্ষিণে, কখনো বামে ইনিই চিরদিন রহিয়া গেছেন, দেখা আর হয় নাই। এবার ফিরিবার পথে সে ক্রটি আর কিছুতে হইতে দিব না, এই ছিল আমার পণ। দিল্লী পরিত্যাগের আয়োজন করিতেছি, শ্রীমান মন্টু অথবা দিলীপকুমার রায় ব্যস্ত-ব্যাকুলভাবে আমার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার গলা ভাঙ্গা এবং চোখের দৃষ্টি অত্যন্ত সচেতন। বাসায় তিনি কান খাড়া করিয়াই রহিলেন। অনুমান ও কিছু কিছু জিজ্ঞাসাবাদের দ্বারা বুঝা গেল, এই কয়দিনেই দিল্লীর লোকে তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিয়াছে, তাই আত্মরক্ষার আর কোন উপায় না পাইয়া অপেক্ষাকৃত এই নির্জন স্থানে আসিয়া তিনি আশ্রয় লইয়াছেন। আমার বৃন্দাবন-যাত্রার প্রস্তাবে তিনি তৎক্ষণাৎ সঙ্গে যাইতে স্বীকার করিলেন। বৃন্দাবনের জন্য নয়, দিল্লী ছাড়িয়া হয়ত তখন ল্যাপল্যাণ্ডে যাইতেও মন্টু রাজী হইতেন। আর একজন সঙ্গী জুটিলেন শ্রীমান সুরেশ,—কাশীর ‘অলকা’ মাসিকপত্রের প্রতিষ্ঠাতা। স্থির হইল বৃন্দাবনে আমরা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে গিয়া উঠিব, এবং সুরেশচন্দ্র একদিন পূর্বে গিয়া তথায় আমাদের বাসের বিলি-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া রাখিবেন।
দিল্লী হইতে শ্রীবৃন্দাবন বেশি দূর নয়। শুভক্ষণ দেখিয়াই যাত্রা করিয়াছিলাম, কিন্তু পথিমধ্যে আকাশ অন্ধকার করিয়া বৃষ্টি নামিল। মথুরা স্টেশনে নামিতে জিনিসপত্র সমস্ত ভিজিয়া গেল, এবং বৃন্দাবনের ছোট গাড়িতে গিয়া যখন উঠিলাম তখন টিকিট কেনা হইল না। আধ-ঘণ্টা পরে সাধের বৃন্দাবনে নামিয়া গাড়ি পাওয়া গেল না, কুলিরা অত্যধিক দাবী করিল, টিকিট-মাস্টার জরিমানা আদায় করিলেন, একগুণ মোটঘাট ভিজিয়া চতুর্গুণ ভারী হইয়া উঠিল এবং পায়ের জুতা হাতে করিয়া সিক্ত বস্ত্রে ক্লান্ত দেহে যখন সেবাশ্রমের উদ্দেশে যাত্রা করা গেল, তখন সন্ধ্যা হয়-হয়; এবং ওয়াকিবহাল এক ব্যক্তিকে আশ্রমের সন্ধান জিজ্ঞাসা করায় সে নিঃসংশয়ে জানাইয়া দিল যে, সে একটা জঙ্গলের মধ্যে ব্যাপার, তথায় যাইবার কোন নির্দিষ্ট রাস্তা নাই এবং দূরত্বও যেমন করিয়া হউক ক্রোশ-দুয়ের কম নয়। মন্টু কাঁদ-কাঁদ হইয়া উঠিল এবং আমার বাহন ভোলা প্রায় হাল ছাড়িয়া দিল। কিন্তু উপায় কি? জলের মধ্যে এই পথের ধারেও ত দাঁড়াইয়া থাকা যায় না; কোথাও ত যাওয়া চাই, অতএব চলিতেই হইল। বৃষ্টি থামার নাম নাই, প্রভূত রজ ছিট্কাইয়া মাথায় উঠিয়াছে, শ্রীকণ্ঠকে পদতল ক্ষত-বিক্ষত, রাত্রি সমাগতপ্রায়, এমনি অবস্থায় দেখা গেল, শ্রীমান সুরেশচন্দ্র একটা চালার আবরণ ভেদ করিয়া বাহির হইতেছে। সে একদিন আগে আসিয়াছে, সে সব জানে, তাহার এইপ্রকার আকস্মিক অভ্যাগমে আমাদের মধ্যে যেন একটা আনন্দ-কলরব উঠিয়া গেল। অপরাহ্ণ-শেষের স্বল্পালোকে দূর হইতে তাহার চেহারা ভাল দেখা যায় নাই, কিন্তু কাছে আসিলে দেখা গেল, মুখ তাহার ভোলার চেয়ে, এমন কি, মন্টুর চেয়েও অধিকতর মলিন। সুরেশ ছেলেটির বয়স কম, কিন্তু এই অল্পবয়সেই সে জ্ঞান লাভ করিয়াছে যে, সংসার দুঃখময়, এখানে প্রফুল্ল হইয়া উঠিবার অধিক অবকাশ নাই। সে গম্ভীর ও সংক্ষেপে সংবাদ দিল যে, বৃন্দাবন কলেরায় প্রায় উজাড় হইয়াছে এবং যে দু-চারজন অবশিষ্ট আছে, তাহারা ডেঙ্গুতে শয্যাগত। কাল সে সেবাশ্রমেই ছিল, সেখানে বামুন নাই, চাকর পলাইয়াছে, ব্রহ্মচারীরা সব জ্বরে মর-মর। গোটা-সাতেক কুকুর আছে, একটার ল্যাজে ঘা, একটা মস্ত রামছাগল আছে তার নাম রামভকত, সে রাজ্যসুদ্ধ লোককে গুঁতাইয়া বেড়ায়। সেবাশ্রমের স্বামীজী বেদানন্দ শুধু ভাল আছেন, আজ তিনি রাঁধিয়াছেন এবং সুরেশ নিজে বাসন মাজিয়াছে। গরম চায়ের আশা ত সুদূরপরাহত, রাত্রে দুটা ভাত পাওয়াই শক্ত। পাশে চাহিয়া দেখিলাম, ভোলা ঊর্ধ্বমুখে বোধ করি তাহার দেশের জগবন্ধু স্মরণ করিতেছে এবং শ্রীমান মন্টুর চোখ দিয়া জল পড়িতেছে। ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া আমরা আবার গন্তব্যস্থানের অভিমুখেই প্রস্থান করিলাম, কিন্তু সমস্ত পথটায় কাহারও মুখে আর কথা রহিল না।
যথাকালে সেবাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অধ্যক্ষ স্বামীজী বেদানন্দ আমাদের সানন্দে ও সমাদরে গ্রহণ করিলেন। গরম চা পাইতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। কারণ, চাকর না থাকিলেও একজন নূতন দাসী আসিয়াছে। বামুন ঠাকুর কি-একটা অছিলায় দিন-দুই পলাতক ছিল, সেও ভাগ্যক্রমে আজ বিকালে আসিয়া হাজির হইয়াছে। সাতটা কুকুরের কথা ঠিক। একটার ল্যাজেও ঘা আছে বটে।
রামভকত গুঁতায় সত্য, কিন্তু সে কেবল মেয়েদের—পুরুষদের সহিত তাহার খুব ভাব। সুতরাং আমাদের আশঙ্কা নাই। আশ্রমের একজন ব্রহ্মচারী পুরানো ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগিতেছিলেন, কাল তিনি পথ্য পাইবেন। একজন বৈষ্ণবী নব-পরিক্রমা হইতে ফিরিবার পথে কলেরায় আক্রান্ত হইয়াছিল, দিন-দুই হইল তাহার শ্রীবৃন্দাবনলাভ হইয়াছে, এ খবর যথার্থ। সমস্ত পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় এ-শহরেও ডেঙ্গু দেখা দিয়াছে, এ সংবাদও মিথ্যা নয়। অতএব শ্রীমান্ সুরেশকে দোষ দেওয়া যায় না।
শহরের একান্তে যমুনাতটে পনর-কুড়ি বিঘার একখণ্ড ভূমির উপর এই সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত। বছর দশ-বার পূর্বে এই বাঙ্গালাদেশেরই একজন ত্যাগী ও কর্মী যুবক কেবলমাত্র নিজের অদম্য শুভেচ্ছাকেই সম্বল করিয়া, এই সেবাশ্রম স্থাপিত করিয়া তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আজ এই প্রতিষ্ঠানটির সহিত আপনাকে তিনি বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু ইহার প্রত্যেক ইট ও কাঠের সহিত তাঁহার বিগত দিনের কর্ম ও চেষ্টা নিত্য বিজড়িত হইয়া আছে। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না, মনে মনে তাঁহাকে শত ধন্যবাদ দিয়া এই রাত্রেই আবার সকলে মন্দিরাদি দেখিতে বাহিত হইয়া পড়িলাম। স্বামীজী আমাদের পথ দেখাইয়া চলিলেন। বৃষ্টি থামিয়াছে, কিন্তু আকাশ তখনও পরিষ্কার হয় নাই। অধিকাংশ মন্দিরের ভিতরের কাজ শেষ হইয়া তখন দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে,—দেখিবার বিশেষ কিছু নাই। লণ্ঠন লইয়া রাস্তা চলিতে হয়,—শ্রীকাদায় ও মাঠের ধোয়া শুক্নো গোক্ষুরফলের তিনকোণা শ্রীকাঁটায় পথ পরিপূর্ণ, স্বামীজী বারবার করিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমরা শ্রান্ত, আজ থাক;—কিন্তু থাকি কি করিয়া? শ্রীমান্ সুরেশের বৃন্দাবন-কাহিনী যে রায়বাহাদুর জলধর সেনের হিমালয়-কাহিনীর মত একেবারে অতখানি সত্য নয়,—এই আনন্দাতিশয্য ঘরের মধ্যে আজ আবদ্ধ করিয়া রাখি কি দিয়া ? পারিলাম না। আলো হাতে সত্য সত্যই বাহির হইয়া পড়িলাম।
অথচ, না গেলেই হয়ত ভাল করিতাম। পথ চলার দুঃখের কথা বলিতেছি না, সে ত ছিলই। কিন্তু সেই আবার পুরাতন ইতিহাস। শুনিতে পাইলাম, এখানে ছোট-বড় প্রায় হাজার পাঁচেক মন্দির আছে। কিন্তু অধিকাংশই আধুনিক,—ইংরাজ আমলের। ইংরাজের আর যাহাই দোষ থাক, যে মন্দিরের প্রতি তাহার বিশ্বাস নাই তাহারও চূড়া ভাঙ্গে না। যে-বিগ্রহের সে পূজা করে না তাহারও নাক-কান কাটিয়া দেয় না। অতএব যে-কোন দেবায়তনের মাথার দিকে চাহিলেই বুঝা যায়, ইহার বয়স কত।
স্বামীজী দেখাইয়া দিলেন, ওটি ওমুক জীউর মন্দির সম্রাট আওরঙ্গজেব ধ্বংস করিয়াছেন, ওটি ওমুক জীউর মন্দির ওমুক বাদশাহ ভূমিসাৎ করিয়াছেন, ওটি ওমুক দেবায়তন ভাঙ্গিয়া মস্জেদ তৈরি হইয়াছে; ওখানে আর কেন যাইবে, আসল বিগ্রহ নাই,—নূতন গড়াইয়া রাখা হইয়াছে,—ইত্যাদি পুণ্যময় কাহিনীতে চিত্ত একেবারে মধুময় করিয়া আমরা অনেক রাত্রে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম। পথে সুরেশচন্দ্র নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—যাক্, সে অনেককালের কথা।
স্বামীজী কহিলেন, কালের জন্য আসিয়া যায় না সুরেশ, মন্দির ভাঙ্গিয়া মস্জেদ ও বিগ্রহ দিয়া সিঁড়ি তৈরির সুযোগ আর নাই,—এই যা তোমাদের ভরসা। তোমরা কংগ্রেসের দল ইংরাজ-রাজার এই গুণটা অন্ততঃ স্বীকার করো।
এই বৃন্দাবনে এক মারবাড়ী ধনী কানা খোঁড়া কালা অন্ধ খঞ্জ সমস্ত বৈষ্ণবীদেরই বৈকুণ্ঠে চড়িবার এক অদ্ভুত লিফ্ট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন শুনা গেল। সুরেশচন্দ্র ত এই মারবাড়ীর ধর্মপ্রাণতায়, বুদ্ধির সূক্ষ্মতায় ও ফন্দির অপরূপত্বে একপ্রকার মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। দেখা হওয়া পর্যন্ত ত এই কথাই সে আমাদের এক-শ’বার করিয়া বলিতে লাগিল, এবং পরদিন সকাল হইতে না হইতে আমাদের সে সর্বকর্ম ফেলিয়া সেইদিকে টানিয়া লইয়া গেল। একটা ঘেরা জায়গায় নানা বয়সের শ’-দুই-তিন বৈষ্ণবী সারি দিয়া বসিয়াছে, প্রত্যেকের হাতে এক-এক জোড়া খঞ্জনী। তাহারা সেই বাদ্য-যন্ত্র সহযোগে সুর করিয়া অবিশ্রাম আবৃত্তি করিতেছে—নিতাই গৌর রাধে শ্যাম, হরে কৃষ্ণ হরে রাম। তাহাদের মাঝখান দিয়া পথ। দুই-তিনজন মারবাড়ী কর্মচারী অনুক্ষণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিয়াছে—কেহ ফাঁকি না দেয়। এইভাবে প্রত্যহ বেলা এগারোটা পর্যন্ত তাহারা বৈষ্ণবী ধর্ম পালন করিলে আধ সের করিয়া আটা পায়, এবং সন্ধ্যাকালে এইমত রুটিনে পরকালের কাজ করিলে এক আনা করিয়া পয়সা পায়। প্রভাতকাল। জন-দুই বুড়া বৈষ্ণবীর তখন পর্যন্ত ঘুম ছাড়ে নাই, তাহারা ঢুলিতেছিল, একজন আধা-বয়সী বৈষ্ণবী তাহার পাশের বৈষ্ণবীর সহিত চাপা-গলায় তুমুল কলহ করিতেছিল। আমরা হঠাৎ প্রবেশ করিতেই বৃদ্ধা দুইটি চমকিয়া উঠিয়া নামগান শুরু করিল এবং যাহারা বিবাদ করিতে ব্যস্ত ছিল, তাহাদের অসমাপ্ত কোন্দল এইপ্রকার আকস্মিক বাধায় বুকের মধ্যে যেন পাক খাইয়া ফিরিতে লাগিল। বিরক্তি ও ক্রোধে মুখ তাহাদের কালো হইয়া উঠিল।
সেই ক্রুদ্ধ মুখের নামকীর্তন ভাগ্যে গিয়া গৌর-নিতাইয়ের কানে পৌছায় না! জন-কয়েক কম-বয়েসী চালাক বৈষ্ণবী দেখিলাম, তালে তালে শুধু হাঁ করে এবং ঠোঁট নাড়ে। চেঁচাইয়া শক্তি ক্ষয় করে না। কিন্তু সকলের মুখে-চোখেই ঠিক পাউন্ডে আটকানো গরু-বাছুরের ন্যায় অবসন্ন করুণ চাহনি। দেখিলে ক্লেশ বোধ হয়। মারবাড়ীরা কিন্তু অত্যন্ত উৎফুল্ল। তাহারা নিজেদের সদনুষ্ঠানের কথা সগর্বে বারংবার বলিতে লাগিল। আর একটা ইঙ্গিতও প্রকারান্তরে করিতে ছাড়িল না যে, কোন একটা উপায়ে ইহাদের আবদ্ধ না রাখিতে পারিলে অসৎপথে যাইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা।
সম্ভাবনা ত আছেই। তথাপি, ফিরিবার পথে আমাদের কেবলই মনে হইতে লাগিল, ইহার প্রয়োজন ছিল না,—এই ফন্দি অসাধু! ধর্ম বস্তুটাকে এমন করিয়া উপহাস করা অন্যায়! ছলে, বলে, কৌশলে মানুষকে ধার্মিক করিতেই হইবে—ইহা কিসের জন্য? এই যে মারবাড়ী ধনী কতকগুলি নিরুৎসুক উদাসীন বুভুক্ষু প্রাণীকে আহারের লোভে প্রলুব্ধ করিয়া ভগবানের নাম-কীর্তনে বাধ্য করিয়াছে, ইহার মূল্য কতটুকু? অথচ, এইরূপ জবরদস্তির দ্বারাই ধর্মচর্চায় নিরত করা সকল ধর্মেরই একটা প্রচলিত পদ্ধতি। কোনটা বা ব্যক্ত, কোনটা বা গুপ্ত, এই যা বিভেদ। এবং মারবাড়ী প্রসন্নচিত্তে ইহাই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে মাত্র। এই ব্যক্তিকেই আর একদিন প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তোমরা এত খরচ কর, কিন্তু সেবাশ্রমে সাহায্য কর না কেন? সে স্বচ্ছন্দে জবাব দিল, সেবাশ্রমের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা ঔষধ দেয়, যে-সে জাতের মড়া ফেলে, রোগীর সেবা করে—এইসব কি সাধুর কাজ? সাধু সুদ্ধাচারী হইবে, ভজন-সাধন করিবে, তবেই ত সে সাধু।
মনে মনে বলিলাম, তাই বটে! তা না হইলে আর আমাদের এই দশা!
নারীর লেখা
নাক ডাকিতেছিল বলিয়া জাগাইয়া দিলে পুরুষমানুষ অপ্রতিভ হইয়া পাশ ফিরিয়া শোয়। মুখে স্বীকার করে না,—হয়ত বা, মনে মনে রাগও করে। এবং মিনিট-দুই পরেই এ-পাশ ফিরিয়া যাহা করিতেছিল ও-পাশ ফিরিয়াও তাহাই করিতে থাকে। এটা পুরুষের স্বভাব। কিন্তু স্ত্রীলোক একেবারে মারিতে আসে। দিব্যি করিয়া বলে, কক্ষণ না; যে যাই বলুক ও-দোষটি তাহার নাই—নাক তাহার ডাকিতেই পারে না। অতঃপর তর্ক নিষ্ফল। করিলে কলহ হয়—আর কিছু হয় না। ঘুমন্ত অবস্থায় একটুখানি শব্দ করিয়া শ্বাস গ্রহণ করিয়াছিল বলায় যে মারাত্মক অপবাদ দেওয়া হয় না, এ কথা স্ত্রীলোক অপরের বেলায় যত সহজেই বুঝুক নিজের বেলায় বোঝে না। এটি তাহাদের স্বভাব।
সুতরাং, আমার বক্তব্য যদি তাহাদের নিকটে অবোধ্য রহিয়াই যায়, তাহাতে বিশেষ আশ্চর্য হইব না। ইহার প্রায় জোড়া আর একটা ব্যাপার আছে—সেটা অনুকরণ করা। পূর্বেরটা শরীরের ধর্ম, পরেরটা মনের। অতএব, অনিচ্ছাতেও যেমন নাক ডাকে, ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও তেমনি অনুকরণ করা হয়। ‘ডাকানো’ অর্থে যেমন ইচ্ছা করিয়া ডাকান নয়, ‘অনুকরণ করা’ মানে ইচ্ছা করিয়াই করা এমন অর্থ না হইতেও পারে। অথচ, নাক ডাকিতেছিল বলিলে খুশী হই না, কেন করিতেছিলাম দেখাইয়া দিলেও কৃতজ্ঞতায় বুক ভরিয়া উঠে না। এসব জানি, কিন্তু একটু সতর্ক হইয়া পাশ ফিরিয়া শোওয়া কি উচিত নয়? এখন কথা যদি উঠে, এ দুইটার কোনটার উপরে সত্যই যদি হাত নাই, এবং ইচ্ছা করিয়াও করি না, এবং দেহ-মনের ইহারা অতি স্বাভাবিক ক্রিয়াই হয়, তবে লজ্জা পাওয়াই বা কেন, আর লজ্জা দেয়ই বা কে! অবশ্য, লজ্জা পাওয়া না-পাওয়া স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু লজ্জা দিবার অধিকার তাহার আছেই, যে ব্যক্তি তখনও জাগিয়া আছে এবং ডাকের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া বিশ্রামের অবসর পাইতেছে না। সুতরাং, স্বেচ্ছায় করিতেছি না বলিলেই সংসারে সব জিনিসের যে জবাবদিহি হয় না, এ কথা তাহাকে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক, যে লোক ঘুমাইতেছে এবং যে লোক নকল করার মধ্যে একেবারে মগ্ন হইয়া গিয়াছে। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, শ্বাস-প্রশ্বাসের চলিত প্রথাটা অতিক্রম করিয়া গেলেও লোক বিরক্ত হয়, এবং ভাল জিনিসের অনুকরণ কর্তব্য এবং স্বাভাবিক হইলেও তাহার নির্দিষ্ট সীমা ডিঙাইয়া গেলেও লোকে নিন্দা করে।
ভাল’র অনুকরণ করিও না, এমন কথা বলিবার অধিকার নিশ্চয়ই কাহারো নাই। কিন্তু, “আর না,—থামো!” এ কথা বলিবার অধিকার সমাজের লোকের আছেই। একটা দৃষ্টান্ত দিই,—
মিসেস বিশ্বাসের পোশাকের কাট-ছাঁট অতি চমৎকার। তেমনি পোশাকে নিজেকে সজ্জিত করিতে দোষ নাই, কিন্তু তাঁর কোমরের ঘেরটা হয়ত সওয়া-তিন হাত। গাউনে কাপড় লাগে সাড়ে-দশ গজ। হুবহু নকল করিব বলিয়া তোমার কাঠপানা দেহে ঠিক ঐ সাড়ে-দশগজি গাউন জড়াইয়া পথে বাহির হইলে লোকে হাসিবে বৈ কি ! ভাল জিনিসের অনুকরণ করিতে গিয়া তুমি ভাল কাজেরই সূত্রপাত করিয়াছিলে মানি, কিন্তু অনুকরণের নেশায় এমনি মাতিয়া গেলে যে, নিজের দেহটার পানেও একবার চাহিয়া দেখিলে না ! ইহাতে তোমার যে শুধু নকল করিবার সদুদ্দেশ্যটাই নিষ্ফল হইয়া গেল তাহা নহে, তোমার নিজের সৌন্দর্যও গেল, তোমার কাপড়ের দাম ও মজুরি নষ্ট হইল। পথের লোকের ‘বাহবাটা’ ত ফাউ। রবিবাবুর লেখা খুব ভাল। তাঁকে নকল করার ইচ্ছাও স্বাভাবিক, এবং করিবার চেষ্টাও সাধু। কিন্তু, একেবারে রবিবাবুই হইবে এমন পণ করিতে গেলে চলিবে কেন? দেখিতে পাওয়া উচিত যে, তোমার গায়ে তাঁর সাড়ে-দশগজি গাউন সার্কাসের ঐ কাহাদের মতই মানাইয়াছে। তাঁর লেখার দোষই বল, আর গুণই বল, পড়িলেই মনে হয় এ ত খুব সোজা। লিখিলে আমিও এমন পারি। তাঁর উপমাগুলা এতই স্বাভাবিক এবং সরল যে দেখিবামাত্রই মনে হয়— বাঃ—এ ত আমিও জানি—উপমা দিবার প্রয়োজন হইলে ঠিক এইটি ত আমিও দিতাম। কিন্তু ভ্রান্ত অনুকরণ-প্রয়াসীরা ভাবিয়াও দেখে না যে, কোহিনুরের নকল হয় না—টেটের ডায়মন্ড হয়। আসলটা পাইলে সাত পুরুষ রাজার হালে বসিয়া খাইতে পারে, নকলটার দামে একবেলার বাজার খরচও চলে না।
রবিবাবু কতকগুলা শব্দ প্রায়ই ব্যবহার করেন। সেইগুলা এবং তাঁহার উপমা ও লিখিবার প্রণালী আজকালকার সাহিত্যসেবী নর-নারীরা কিরূপে যে বিকৃত করিতেছেন, তাহা দেখিলে ক্লেশ বোধ হয়।তিনি যাঁহাদের গুরু, তাঁহাদের উচিত তাঁকে বুঝিবার চেষ্টা করা, তাঁকে শ্রদ্ধা করা। ভিতরে ভিতরে ইঁহারা শ্রদ্ধা করেন কিনা, এ কথা অবশ্য বলিতে পারি না; কিন্তু বাহিরে ভ্যাঙচানির চোটে গুরুজীর হাড় পর্যন্ত যে কালি হইবার উপক্রম হইয়াছে, সে কথা বাজি রাখিয়া বলিতে পারি। সে বেচারা যাই বলেন, ব্যাঘ্র ! তাঁর ভক্তেরা অমনি ছুটিয়া আসিয়া দুই হাত নাড়িয়া বুঝাইয়া দিয়া যায়—অর্থাৎ, শার্দুল ! দুই-একটা নজির দিতেছি। অবশ্য পুরুষদের কথা বলিতে চাহি না।
তাঁহাদের কথা তাঁহারাই বলিবেন—এবং মাঝে মাঝে কেহ বলেনও, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। ঐ ডান পাশ আর বাঁ পাশ। আমি শুধু দুই-একটি মহিলা সরস্বতীর কথা উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইব।
আজকাল যাঁহারা বড় লিখিয়ে হইয়া উঠিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষজায়া, অনুরূপা ও নিরুপমা দেবীর নাম প্রায় সকলেই জানেন। ইঁহাদের অজস্র গদ্য পদ্য কোন একখানা মাসিক হাতে তুলিয়া লইলেই দেখিতে পাওয়া যায়। আজ ইঁহাদের কথাই বলি। শ্রীমতী ঘোষজায়ার লেখা নাকি রবিবাবুর লেখা বলিয়া অনেকের ভ্রমও হয়। অবশ্য ভ্রমের হেতুও আছে।
আমি পূর্বেই বলিয়াছি, রবিবাবুর সত্য অনুকরণ যত কঠিনই হউক, বিকৃত করা খুব সহজ। ও আর কিছু নয়—আমার নিম্নলিখিত এই তালিকাটি মুখস্থ করিলেই হইবে। যদি মুখস্থ না হয়, বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া টেবিলের সম্মুখে টাঙাইয়া দিয়া নিজের রচনার মধ্যে মধ্যে এক একটা প্রবেশ করাইয়া দিলেই কাজ হইবে। হরির লুটের বাতাসা কোঁচড়েই পড়ুক, আর পায়ের নীচেই পড়ুক, নিষ্ফল হইবে না। মুখস্থ করুন—পরিণতি, বিশ্ব, মানব, দেহান্বয়, ভূমিষ্ঠ, গরিষ্ঠ, মুখর, চাই-ই, বনস্পতি, প্রয়োজন হইয়াছে, ফাঁকি, দৈন্য, পুষ্টি-সাধন, দেবতা, অমৃত, শ্রেয়, ভূমা, আশীর্বাদ, অর্ঘ্য, আবহমানকাল, শ্রেষ্ঠ, বাণী, খাঁটি, ভারতবর্ষ, নিষ্ঠা, জাগ্রত, জন্মস্বত্ব, দিন আসিয়াছে, তপশ্চর্যা, বৈরাগ্য, শ্রদ্ধা, যো-নাই, খাটো, পাৎলা, ডাক পড়িয়া গিয়াছে, মুক্তির আনন্দ ও ত্যাগের আনন্দ। বাস, এই কয়টিই যথেষ্ট। একটা রচনার মধ্যে সব ক’টা ব্যবহার করিতে পার উত্তম, না পার ভূমা, অর্ঘ্য, দেবতা, বৈরাগ্য ও ভারতবর্ষ এই পাঁচটি চাই-ই। অন্যথা রচনাই নয়। এখন কেহ যদি অবিশ্বাস করিয়া বলেন, তা কি হয়? শব্দগুলা যদৃচ্ছা গুঁজিয়া দিলে লোকে ধরিয়া ফেলিবে যে! ইহার উত্তরে আমার নজির দেওয়া ছাড়া আর উপায় নাই। গত অগ্রহায়ণের ভারতীতে শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষজায়ার আট পাতা জোড়া এক প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। নাম ‘মনুষ্যত্বের সাধনা’। টাইটেল দেখিয়াই ‘বাপ্রে!’ করিয়া উঠিলে চলিবে না। ভক্তি করিয়া পড়া চাই। আমার তালিকার প্রায় সকল শব্দগুলাই ইহাতে আছে, সুতরাং ইহা খুব ভাল, এবং শিক্ষা হইবে। তবে, অভিধানের সাহায্যে সবটুকু পড়িয়া কেহ যদি শেষকালে বলেন, এই আট পাতার ত আট ছত্রেরও মানে হয় না, তাহা হইলে আমি চুপ করিয়া থাকিব বটে, কিন্তু কবুল করিব না, এবং মনে মনে রাগ করিয়া বলিব, তবু তোমার শিক্ষা হইল ত!
যাহা হউক, আমি নজির দিব বলিয়াছি, কিন্তু সমালোচনা করিব বলি নাই। সমালোচনা করা পণ্ডশ্রম। আমি বলিব, তোমার রচনার মানে নাই; তুমি জবাব দিবে, ‘আছে’। আমি বলিব, এই জায়গাটায় বাড়াবাড়ি করিয়াছ; তুমি বলিবে, ‘একটুও না; এমন না করিলে লেখা ফুটিত না’। আমি বলিব, ‘এই স্থানটার আর একটু প্রকাশ করা উচিত ছিল’; তুমি বলিবে, ‘নিশ্চয় না; আর প্রকাশ করিতে গেলে আর্ট মাটি হইয়া যাইত।’ বাস্তবিক, এ-সব তর্কের মীমাংসা হয় না। একেই লেখা বলে এই বিবেচনার উপরেই লেখকের যথার্থ কৃতিত্ব নির্ভর করে। সমালোচনা করিয়া দোষ-গুণ দেখাইয়া নিন্দা বা সুখ্যাতি করা যায় বটে কিন্তু আর কোন কাজ হয় না।
যাহা হউক, যাহা বলিতে চাহিয়াছিলাম তাহাই বলি। উক্ত প্রবন্ধে শ্রীমতী ঘোষজায়া বলিতেছেন, “ভারতবর্ষ অকস্মাৎ আজ স্বপ্ন হইতে জাগিয়া দেখিতেছে, যে জনপদের পথ ধরিয়া সে চলিতেছিল তাহা প্রকৃত নয়, মায়া সৃষ্টি মাত্র, অকস্মাৎ আজ তাহা দিগন্তবিলীন বাণীর ভিতর কোথায় মিলিয়া গিয়াছে।” ভাষা বটে! জনপদের পথ দিগন্তবিলীন বাণীর মধ্যে মিশিয়া গেল! জিজ্ঞাসা করি, রবিবাবু কোথাও কি এমনি করিয়া ‘বাণীর’ শ্রাদ্ধ করিয়াছেন? কিছুদিন পূর্বে লেখিকা ‘বিকাশ’ পত্রিকায় একটি দশ-বারো লাইনের কবিতায় ‘ব্যোম’ -এর সঙ্গে মিলাইবার জন্য ‘শশি সূর্য্য সোম’ লিখিয়াছিলেন। কবিতার কথা না হয় নাই ধরিলাম—কেন না, ‘ব্যোম’-এর ‘ম’ ‘সোম’ ছাড়া মিলিতে চায় না। ‘শশী’টিকেও বাদ দিলে অক্ষর কম পড়ে। কিন্তু, জনপদের পথের ত অমন কোন ধনুকভাঙ্গা পণ ছিল না যে, ঐ ‘বাণী’টি না পাইলে আর মিলিত না! কবিকে অঙ্কুশ দেখাতে নিষেধ আছে তাহা মানি, কিন্তু তার্কিক যখন ঘর ছাড়িয়া লাঠি-হাতে মারিতে আসে তখনও যে একটুখানি আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে নাই এ কথা মানি না। সেটা ‘কাব্যি’! কিন্তু এটা যে দার্শনিক প্রবন্ধ! দার্শনিক প্রবন্ধ যখন এক শ’ টাকা দাবী করে, তখন সে ঐ ক্ষুদ্র তিনটি অক্ষরের ‘এক শ’ টাকাই চাই, তাহাকে ‘নব-নবতি রজত-মুদ্রা’ দিতে গেলে সে হাত পাতিয়া গ্রহণ করে না। কিন্তু আসল কথা এই যে, ‘বাণী’ রবিবাবু লেখেন, সুতরাং সেটা চাই-ই।
যদিও নাটক-নভেলে অত দোষ নাই, তথাপি অনুরূপা ‘পোষ্যপুত্রে’ লিখিলেন “পথে শব্দ মুখর হইয়া উঠিল” তখন ‘শব্দ’ শব্দায়মান হইয়া উঠিল বলা নিশ্চয়ই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না, কিন্তু ‘মুখর’ কথাটার ঠিক মানেটাও ত তাঁর জানা উচিত ছিল। জোর করিয়া ‘নির্লজ্জ’ অর্থ করার চেয়ে বরং বলা ভাল, “কি করিব ওটা যে আমার চাই-ই। ওটা মহতের ইত্যাদি।”
শ্রীমতী অনুরূপা আর একস্থানে লিখিতেছেন—“ক্ষেত্র কর্ষিত হইলে শস্য দান করে, পতিত থাকিলে কণ্টক-গুল্মের আবাসভূমি হয়। সুতরাং ভারতবর্ষের নৈতিক ক্ষেত্রও আকর্ষণে যে কণ্টক-গুল্মে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিবে, ইহা কোন স্বভাব-বিরুদ্ধ ব্যাপার নহে। বনস্পতি এ-কাননে পূর্বে বিদ্যমান ছিল বটে, কিন্তু এখন তাহা বল্মীক ও লতাস্তূপে এমন করিয়া ঢাকিয়া পড়িয়াছে, তাহাকে আর চিনিয়া বাহির করিবার বুঝি কোন উপায় নাই।” ছিল ক্ষেত্র এবং শস্য, আসিল কানন ও বনস্পতি। তা আসুক—ক্ষেত্র না হয় বন-জঙ্গল হইতেও পারে, কিন্তু কোন শস্যকেই ত বনস্পতি হইয়া উঠিতে দেখিলাম না। এদিকে ত হয় না—ও-দিকে হয় কিনা বলিতে পারি না। ওদিকে বোধ করি হয় না; কিন্তু ‘বনস্পতি’টি যে চাই-ই। কিন্তু, আমি বলি চাহিবার পূর্বে ও জিনিসটা যে মটর-কলায়ের গাছ নয়, এটা ত জানা উচিত ছিল। এই মহতের আশ্রয় ধরিতে গিয়া অনুরূপা একস্থানে লিখিলেন, “ভূমার সঙ্গে ভূমির, ক্ষুদ্রের সঙ্গে মহতের এই যে যোগ!” অর্থাৎ, ছোট্ট ভূমিটি মহৎ ভূমির সঙ্গে যুক্ত হইতেছে। ‘ভূমা’ কথাটা যে ব্যবহার করা আবশ্যক, আমি তাহা অস্বীকার করি না, কিন্তু কোন্টি ক্ষুদ্র, কোন্টি মহৎ সে সংবাদটাও কি বই লেখার পূর্বে অনুসন্ধান করা আবশ্যক ছিল না?
১৩১৭ সালের আষাঢ়ের ভারতীতে ‘প্রাচীন ভারতের পূজায়’ শ্রীমতী ঘোষজায়া লিখিয়াছেন,—“আত্মসম্মানের সঙ্গে আত্মসম্মানের সঙ্গে আত্মদানের একটা সাদৃশ্য আছে, এই সাদৃশ্য-সঙ্কট এড়াইবার জন্য, ভারতবর্ষের ধর্মনীতি আত্মসম্মানকে দূরে রাখিয়া আসিয়াছে। ফল যখন পাকে, তখন আপনা হইতেই বোঁটা ছাড়িয়া পড়ে, পাকাইবার জন্য তাহাকে বৃন্তহীন করিলে তাহা বিকৃতই হয়, পরিণত হয় না।” আমি আজ পর্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না, এই ‘বোঁটাছাড়ার’ উপমাটির যোগ কাহার সঙ্গে। মৌলিক না হইলেও স্বতন্ত্রভাবে উপমাটি খুব ভাল তাহা স্বীকার করি, কিন্তু এই আগাগোড়া পরিপূর্ণ সুখ্যাতির মধ্যে ভাল যে এখানে সে কাহার করিতেছে তাহা বুদ্ধির অগোচর। “বাবলার মত সর্ববিসারি গুল্ম”টার ন্যায় ‘অহং’ জিনিসটাকে বারংবার নিন্দা করিয়া তাহাকে পরিবর্জন করিয়া প্রাচীন ভারতবর্ষ যেদিন বিরাট ব্যাপার করিয়াছিল, এবং তাহার প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক বর্ণ তাহার বিরাট রাজছত্রতলে স্থান পাইতেছিল, সেই সময়ে এই জোর করিয়া বোঁটাছাড়া অপরিণত ফলটি যে কোন্ শ্রেণীর মধ্যে ঢুকিতে গিয়া অন্যায় করিয়াছিল তাহা বুঝিয়া লইবার কোন পথই লেখিকা রাখেন নাই।
সেদিন এই প্রাচীন ভারতের সুখ্যাতি ধরিতেছিল না; হঠাৎ এই বৎসর-দুয়েকের মধ্যে সে যে কি অপরাধ করিয়াছে যে, ঘোষজায়া মহাশয়া ‘মনুষ্যত্বের সাধনার’ ছুতা তুলিয়া এমন করিয়া তাহাকে আজ ভর্ৎসনা শুরু করিয়া দিয়াছেন? বলিতেছেন, “কিছুমাত্র না বুঝিয়া শুক ও তোতার মত কণ্ঠস্থ করা যে বিদ্যাধ্যয়ন নহে, তাহা বলা নিশ্চয়ই বাহুল্যোক্তি, অধুনা শিশুশিক্ষাতেও এরূপ মূঢ় নীতি প্রযুক্ত হয় না। কিন্তু আমাদের এই শ্রদ্ধেয়, পূজ্যপাদ, জ্ঞানগরিষ্ঠ ভারতবর্ষ এখনও তাহার ত্রিশ কোটি নর-নারীকে সেই প্রাথমিক যুগের প্রথম পাঠ পড়াইতেছে, গম্ভীর-মুখে মাথা নাড়িয়া সে বলিতেছে, ‘জিজ্ঞাসা করিবার তোমাদের কোন অধিকার নাই, আজ্ঞাবহের মত তোমরা কেবল আজ্ঞা পালন করিবে, ইহাই তোমাদের মুক্তির মূল্য !” জ্ঞানগরিষ্ঠ ভারতবর্ষের এই জ্ঞানের পরিচয় দিয়া পরে লিখিতেছেন, “কিন্তু প্রাচীন ভারত এই আপেক্ষিকতাকে একেবারেই আমল দেয় নাই, নেশার ঝোঁকে অসাধ্য-সাধনের পরম উল্লাসকে সে এমন বড় করিয়া দেখিয়াছিল যে জীবনের ছোটখাট কর্তব্যগুলি একান্তভাবে সে অবজ্ঞা করিয়াছে।” প্রাচীন ভারতবর্ষ নেশা খাইয়া কি করিয়াছিল, এবং জীবনের ছোটখাট কর্তব্যগুলি একান্তভাবে অবজ্ঞা করিয়াছিল কিংবা করে নাই, এ তর্ক তুলিব না। বিদুষীরা যখন বলিতেছেন, তখন মানিয়াই লইলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ওই ‘শ্রদ্ধেয়’ ‘পূজ্যপাদ’ প্রভৃতি বিশেষণগুলার কিছু অর্থ আছে, না, ওগুলো শুধু বিদ্যার পরিচয়? নিজের পিতার কোন ভুলের প্রতিবাদ করিবার জন্য তাঁহার মুখের সামনে দাঁড়াইয়া যদি বলা যায়,“হে আমার শ্রদ্ধেয় পূজ্যপাদ জ্ঞানগরিষ্ঠ বাবা! তুমি তাড়ি খাইয়া নেশার ঝোঁকে মাতলামি করিতেছিলে কি জন্যে?” কেমন শুনায়? কে নাকি বাহিরে মার খাইয়া আসিয়া স্ত্রীর কাছে আস্ফালন করিয়া বলিয়াছিল, “হাঁ, কান মলে দিয়েচে বটে, কিন্তু অপমান করেনি।” ঘোষজায়া মহাশয়াও পূজ্যপাদের অপমান করেন নাই শুধু কান মলিয়াছেন। যাহ হউক লেখার হাত বটে !
একস্থানের ইনি Evolution Theory ব্যাখ্যা করিয়া শেষে বলিতেছেন, “প্রবৃত্তিমার্গের শাসন পালন করিয়া তাহা খণ্ডনপূর্বক যাঁহারা নিবৃত্তি-মার্গে আরোহণ করিয়াছিলেন, বর্তমান ভারত তাহার লুপ্ত পদাঙ্ক পুনরুদ্ধার আর করিতে না পারিয়া অন্তভাগশায়ী অবশিষ্ট চিহ্নগুলিকে একান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছে ও তাহাকে কৃপণের ধনের মত আঁকড়িয়া ধরিয়া রহিয়াছে।
তাহার পিছনে যে বিস্তৃত মুখগহ্বর অন্ধকারে মুখ ব্যাদিত করিয়া আছে, তাহাকে সে শুধু অসম্ভব প্রয়াসের দ্বারা আড়াল করিয়া রাখিতে চাহিতেছে, কিন্তু তাহার পায়ের নীচের মাটি তাহার ভারে যে খসিয়া পড়িতেছে, তাহার প্রতি তাহার দৃকপাত নাই।” অর্থাৎ ‘অন্ধকার গহ্বর’ ‘অসম্ভব প্রয়াস’ ‘পায়ের নীচের মাটি খসিয়া পড়া’ কথাগুলো লাগাইতেই হইবে। কেন তাহা বলা বাহুল্য। কিন্তু গোল হইতেছে এই যে, অন্তভাগশায়ী চিহ্নগুলিকে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকিবার মাঝখানে এত বড় গহ্বরটাই বা আসে কি সুবাদে এবং পায়ের নীচের মাটিই বা খসিয়া পড়ে কি হেতু? গহ্বরটা যে শুধু সে বেচারাই দেখিতে পায় নাই, তাহা নহে, আমরাও ত কৈ কোনদিকে চাহিয়া চোখে পড়িতেছে না। আর একস্থানে রাশি রাশি শাস্ত্রের দোষ দিয়া লিখিতেছেন, “জীবনের অবস্থা-ভেদে কর্তব্য ও ধর্মের প্রভেদ ঘটিয়া থাকে। পুরুষের যাহা ধর্ম নারীর ধর্ম তাহা হইতে পারে না। অপরন্তু,—সন্ন্যাসী যদি গৃহীর ধর্ম অবলম্বন করে, তবে সন্ন্যাসী ধর্মভ্রষ্ট হয়, এবং গৃহী যদি সন্ন্যাসীর পন্থানুসরণ করে, তবে গৃহীও ধর্ম হইতে স্খলিত হয়। …লোকসমাজে যখন একটা অনুভূতির স্পন্দনোচ্ছ্রয় ঘটিতে থাকে, বিধানের চাপ দিয়া তাহাকে বিমর্দিত করা যায় না, গর্জিত স্রোত তরঙ্গিণীর মত তাহা পথশায়ী প্রতিবন্ধক বিধ্বস্ত করিয়া পথ উন্মুক্ত করিয়া লইয়া অবতরণ করে। সুতরাং গৃহীদের সন্ন্যাসনুপন্থী হইবার সম্বন্ধে প্রবল শাস্ত্র-প্রতিষেধ থাকা সত্ত্বেও সমাজে তাহার প্রভাব অণুমাত্রও হ্রাস হয় নাই।”
আমার বিনীত নিবেদন এই, ‘সুতরাং’টির অর্থ কি? সমাজের বিলকুল গৃহীগুলা কি গৃহিণী ত্যাগ করিয়া বনে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছে? না, লুকাইয়া গেরুয়া কাপড় ছোবাইতেছিল, ধরা পড়িয়াছে। হইলে ভয়ের কথা নিশ্চয়ই, কিন্তু আমাদের বাড়িতে কাহারও ত ওসব লক্ষণ দেখি না। অন্ততঃ বড়কর্তার সম্বন্ধে আমি ত হলফ করিয়া বলিতে পারি। আজ এই ‘সুতরাং’ শব্দটায় বহুদিনের একটা কথা মনে পড়িতেছে। একবার গাড়ি করিয়া রাত্রে বাড়ি যাইতেছিলাম। পথে ডানদিকের মাঠে চাষারা পাট কাচিয়া শুকাইতে দিয়াছিল। পাছে ভয় পাই, এই আশঙ্কায় আমাদের পঞ্চা চাকর গাড়ির উপর হইতে সাহস দিয়া বলিল, “মা-ঠাকরুন ডানদিকে চেয়ে দেখুন,সুতরাং কেমন পাট শুকোচ্চে !” সেদিন বউমানুষের অত হাসি নিশ্চয়ই ভাল দেখায় নাই, কিন্তু ভাল দেখাইবার উপায় ত আমার হাতে ছিল না।
থাক্—আর না। এখনো অনেক কথা বলিবার ছিল, কিন্তু কাজ নাই। তা ছাড়া, আমরা মেয়েমানুষ হাঁড়ির একটা ভাতই টিপিয়া দেখি। শ্রীমতী আমোদিনী শিক্ষিতা রমণী, আমরা সেকেলে অশিক্ষিতা মূর্খ মেয়েমানুষ। হয়ত, তাঁহাকে ভুল বুঝিয়াছি। কিন্তু ভুল হোক, নির্ভুল হোক, যাহা বুঝিয়াছি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছি। যদি আবশ্যক হয় নিজের লেখা তিনি অনায়াসে সমর্থন করিতে পারিবেন। তবে, একটা কথা বলিয়া রাখি। মেয়েমানুষের নাক ডাকে জানি, কিন্তু এত জোরে ডাকিতে শুনিলে অন্য স্ত্রীলোকেও যেন লজ্জা করিতে থাকে। ভয় হয়, এই বুঝি বা পুরুষমানুষে চমকাইয়া উঠিয়া পড়ে। তাই উৎকণ্ঠায় যদি বা একটু নিষ্ঠুরের মতই ঘুম ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিয়া থাকি, সে চেষ্টার মধ্যে আন্তরিক মঙ্গলেচ্ছা ব্যতীত আর কিছুই নাই। কিন্তু তাঁর ভাষা যে অতি সুন্দর, অতি মধুর, তাহা অকপটে স্বীকার করি। প্রতি ছত্র গভীর পাণ্ডিত্যে পরিপূর্ণ। বহুমূল্য ঘড়ির সুগঠিত কলকবজার ন্যায় তাঁহার প্রত্যেক শব্দবিন্যাসটির আশ্চর্য কৌশল দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। ঘড়িটি দামী এবং চলিতেছেও। কিন্তু কাঁটা দুটি না থাকায় কবি পোপের মত সময়টা ঠিক ঠাহর করিতে অক্ষম হইয়াছি।
এইবার শ্রীমতী অনুরূপা ও নিরুপমার রচনা সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলিব। যদিও শ্রীমতী অনুরূপার ‘পোষ্যপুত্রে’র গোড়াও পড়ি নাই, শেষও পড়ি নাই, শুধু মধ্যের গুটিকয়েক অধ্যায় মাত্র পড়িবার সুযোগ পাইয়াছি, এবং এত অল্প পুঁজি লইয়া বলিতে যাওয়াও বিপজ্জনক জানি, কিন্তু বুড়ো-মানুষের নাকি বেশি পুঁজির আবশ্যক হয় না, তাই বলিতেছি। ইঁহারও ভাষা যে অতি মধুর তাহাতে সন্দেহ নাই। আমার মেয়ে বলিতেছিল, এত মধুর যে মুখ মারিয়া যায়, আর গিলিতে পারা যায় না। তা’ ভাষা যাহাই হোক, প্রায়ই উপমাগুলিই যে না জানিয়া লেখা তাহা পড়িলেই চোখে ঠেকে। আর একটা জিনিস তার চেয়েও বেশী ঠেকে—সেটা অসহ্য জ্যাঠামো। এ কথা আমার বলিবার ইচ্ছা ছিল না। কেন না, এইখানেই তর্ক বাধে। গ্রন্থকারের তারিফ্কারীরা ধরিয়া বসেন, কোথায় জ্যাঠামো দেখাও। আমি যাহাই দেখাই না কেন, তাঁহারা প্রতিবাদ করিয়া বলিবেন— কখ্খন না। এটা হিউমার, ওটা উইট্, সেটা আর্ট ইত্যাদি।
জ্যাঠামো অন্তরে অনুভব করা যায়, কিন্তু উইট্ কোথায় অশ্লীল হইয়া উঠে, আর্ট কোথায় আতিশয্যে ও ছিবলামিতে রূপান্তরিত হয়, সেটা যে-বয়সে বোঝা যায়, ততটা বয়স এখনও লেখিকার হয় নাই। তবে, আশা করি এ দোষ একদিন শুধরাইবে। কিন্তু, তাঁহার না জানিয়া যা-তা উপমা দিবার স্বপক্ষে সে-রকম কৈফিয়ত কিছু নাই। তাই দৃষ্টান্তের মত দুই-একটা উল্লেখ করিব মাত্র।
একস্থানে বলিতেছেন, “বিজন-পথে চলিতে চলিতে অকস্মাৎ পায়ের নীচে দংশনোদ্যত সর্প দেখিলে পথিক যেমন আড়ষ্ট কাঠ হইয়া দাঁড়ায়, ইত্যাদি।” তাই বটে ! একটা ন্যাকড়া কিংবা দড়ির টুক্রা দেখিলে লাফাইয়া কে কার ঘাড়ে পড়িবে ঠিক থাকে না, আড়ষ্ট হইয়াই দাঁড়ায়! তাও আবার যে-সে সর্প নয়—একেবারে দংশনোদ্যত সর্প! ইনি যে লেখেন নাই, রান্নাঘরে হঠাৎ জ্বলন্ত আগুনের টুকরা পায়ের নীচে মাড়াইয়া ধরিয়া রাঁধুনী যেমন অবাক হইয়া হাঁ করিয়া দাঁড়ায়,—ইহাই পরম ভাগ্য!
আর একস্থানে লিখিতেছেন, “দীপ্ত সূর্য্যালোকের উপর মেঘ আসিয়া পড়িলে তাহা যেমন এক-মুহূর্ত্তেই ম্লান হইয়া যায়, শিবানীর মুখ তেমনি মুহূর্ত্তে অন্ধকার হইয়া আসিল। ”এটা অলঙ্কার না উপমা? কিন্তু দীপ্ত সূর্যালোকের উপর মেঘ আসিয়া পড়িলে কি হয়? সাদা দেখায়। কিন্তু লেখিকা ঐ যে ম্লান বলিয়াছেন, কাজেই তাঁহার অন্ধকার মুখের সহিত সূর্যালোক-পতিত মেঘের তুলনা করিবার অধিকার জন্মিয়াছে! এই কি! আর এক জায়গায় গভীর কৃষ্ণবর্ণ মেঘের গায়ে বক প্রভৃতিকে উড়িতে দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছে যেন ‘কৃষ্ণতারকা’ উড়িয়া যাইতেছে। কালো মেঘের তলায় বক কি কৃষ্ণতারকার মত দেখায়? তা ছাড়া ‘কৃষ্ণতারকা’ই বা কি? রাত্রে আকাশের পানে চাহিয়া কোনদিন ত কালো কুচ্কুচে নক্ষত্র চোখে পড়ে না। আর যদি চোখের তারাই হয়, সেও ত সাদা পদার্থের মাঝখানে থাকে। কালো মেঘের সঙ্গে তাহার সাদৃশ্যই বা কোথায়? প্রকৃতি-দেবীর উপর এই রকমের উৎপাত আরও অনেক আছে—সেইগুলি একটুখানি হুঁশ করিয়া করা উচিত ছিল। কেন না, নিজে যাহা জানি না, তাহা না জানানই বুদ্ধির কাজ।
যা হউক, বইখানি, শুনিয়াছি ৫। ৬শ পাতার; আমি মাত্র ২৫। ৩০ খানি পাতা পড়িয়াছি; সুতরাং আশা করিতেছি, যাহা পড়ি নাই তাহার মধ্যে ভাল ভাল জিনিসই রহিয়া গিয়াছে। মেয়েটাও বলিতেছিল, বইখানি জ্ঞানগর্ভ। বেদ, কোরান, বাইবেল, রামায়ণ, মহাভারত, এথিক্স, মেটাফিজিক্স, রামপ্রসাদী, তন্ত্র, মন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, মারণ, উচাটন, বশীকরণ—সমস্তই আছে।
এ-ছাড়া সংস্কৃত, হিন্দী, ইংরেজী—কালিদাস, সেক্সপিয়র, টেনিসন—যাহা কিছু শিক্ষা করা প্রয়োজন একাধারে সমস্তই। বলিতে পারি না, শেষের দিকে রাজাভাষা এবং Clerk’s Guide আছে কিনা। আমার ছোট নাতিটিকে একখানি কিনিয়া দিব মনে করিতেছি।
যদি আমার রাধারানীর কথা সত্য হয়, তবে, আর গোট-দুই প্রশ্ন করিয়াই ক্ষান্ত হইব। জিজ্ঞাসা করি, এত বাড়াবাড়ি ধর্মচর্চা কেন? হিন্দু ধর্মের অত সূক্ষ্ম ভেদগুলি না হয়, নাই দেখান হইত—তাহাতে এমনিই কি ক্ষতি ছিল! এ যে সন্ন্যাসী ফকিরের ভিড়ে পা বাড়াইবার জো নাই, কোথায় দাঁড়াই, কোন্ দিকে চলি, কোন্ মহাত্মার গায়ে এই বুঝি পা দিয়া ফেলি, এই ভেবেই যে সারা হইতে হয়। তার উপর ইংরেজির বুকনি ও ইংরেজি কবিতার লম্বা কোটেশন! এ কথাও ভাবা উচিত ছিল, এটা বাংলা উপন্যাস এবং তাঁহার অধিকাংশ ভগিনীগুলিই ইংরেজি জানেন না। জানি বলিয়া কি তাহা জানাইতেই হইবে! শুনিয়াছি, রবিবাবুও ইংরেজি জানেন, বঙ্কিমবাবুও নাকি শিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও নভেলের মধ্যে লোভ সংবরণ করিতে পারিয়াছিলেন! এ-ক্ষেত্রেও লোভ সামলান উচিত ছিল। অন্তঃপুরচারিণী স্ত্রীলোক হইয়াও সর্বতোমুখী পাণ্ডিত্যের বহরে লোকজনের তাক্ লাগাইয়া দিব, এই স্পিরিট্টাই নিন্দার্হ। অগ্রহায়ণের ‘ভারতী’তে এক ভদ্রলোক এই বইখানি সমালোচনা করিয়া একস্থানে বলিয়াছেন, স্থানে-অস্থানে অত্যধিক প্রকৃতি-বর্ণনা এবং তাহাতে রসভঙ্গ না কি এমনি একটা দোষ ঘটিয়াছে। আমি কিন্তু এ কথা বলি না। বরং বলি, দুই-তিন পাতা জোড়া প্রকৃতি-বর্ণনা পড়িয়া যে ব্যক্তি একটা কিছু আইডিয়া করিতে চায় সে-ই অরসিক। এ জিনিসটা গয়ায় পিণ্ডি দেবার মত। পুরোহিত ঠাকুরও জানে না, কি বলাইতেছি; যজমানও গ্রাহ্য করে না, কি বলিতেছি! অথচ, উভয়েই জানে কাজ হইতেছে—ভূত ছাড়িতেছে! এ-বিষয়ে শ্রদ্ধা থাকা চাই, বিশ্বাস থাকা চাই; প্রকৃতি-বর্ণনা বুঝিতেছি। ভেলকি-খেলা দেখেন নাই? খেলওয়াড় চোখের ভিতর হইতে হাঁসের ডিম বাহির করিবার আগে হাত-পা নাড়িয়া ভানুমতীর ব্যাখ্যা শুরু করিয়া দেয়—এ তেমনি। বোঝা উচিত, এবার আশ্চর্য কিছু-একটা আসিতেছে। যে সমঝদার সেই জানে এইবার ডিম বাহির হইবে—বোকায় শুধু হাত-পা নাড়া দেখিতেই ব্যস্ত থাকে এবং ভানুমতী ব্যাখ্যার মানে বুঝিতে চায়। আমি ত ৩০ অধ্যায়ের গোড়াতেই বুঝিয়াছিলাম, এবার নতুন কিছু একটা আছে।
লেখিকা লোক-হিতার্থে দয়া করিয়া পেট কামড়ানির মন্ত্র পর্যন্ত শিখাইয়া দিয়াছেন।
“রাম লক্ষ্মণ সীতে যান কিষ্কিন্ধ্যের পথে;
সাথে নিলেন হনুমান আর সুগ্রীব মিতে;
সুগ্রীব বলেন, মিতে আমি মন্তর জানি,
পেটের ব্যথায় অব্যথা হয়ে যায় প্রাণী।”
বাস্তবিক, লোকের কুসংস্কারে হিন্দু-ধর্মের অনেক ভাল জিনিস লোপ পাইতেছে, এটা কোনমতেই হইতে দেওয়া উচিত নয়। শ্রীযুক্ত লালবিহারী দে, গোবিন্দ সামন্তকে সাপের মন্তর শিখাইয়া দিয়াছিলেন। আমিও পেট কামড়ানির একটা মন্তর জানি, যদি কাহারও উপকার হয় তাই লিখিতেছি। অবশ্য আমার মন্তর অব্যর্থ কিনা বলিতে পারি না। এ বাড়ির পুরুষগুলা গোঁয়ার গোছের, ওসব বিশ্বাস করিতে চাহে না—তাই, যাচাই করিয়া লইবার সুবিধা ঘটে নাই—যে বাড়ির পুরুষেরা শিষ্ট শান্ত সেখানে পরখ হইতে পারিবে! মন্তর এই—
“পেট কামড়ানি, পেট কামড়ানি,
ভাল হবি ত হ’;
নইলে কামড়ে কামড়ে কি গরু বাছুর
মেরে ফেলবি!”
রোগীর পেটে হাত বুলাইয়া তিনবার বলিতে হয়।
এবার শ্রীমতী নিরুপমার কথা কিছু বলিব। ইঁহাদের মধ্যে নিরুপমার রচনাকে অনেক দিক হইতেই ভাল বলিতেই হয়। সহজ, সরল ও বিনীত। যাকে ‘পাণ্ডিত্যের হুঙ্কার’ বলে সেটা নাই, এবং স্টেজ আস্ফালনিও কম। কথাবার্তাগুলি কথাবার্তারই মত। লেখায় ভুল যে নাই তাহা নহে। ভুল কাহারই বা না থাকে, এবং থাকিলেই তাহা মহা লজ্জার বিষয় হয় না, যদি না ভুল যাচিয়া ঘরে আনি। যদি না সোজা পথ ছাড়িয়া অজানা পথের মধ্যে গিয়া পথ হারাই! শরীরে ঘা হওয়া এক এবং চুলকাইয়া ঘা করা আর। একটায় মায়া হয়, অপরটায় রাগ করিতে ইচ্ছা করে—মুখে আসিয়া পড়িতে চায়—বেশ হইয়াছে, যেমন কর্ম। যদি পারিবে না, তবে যাও কেন? নিরুপমা এই দোষটি করেন বলিয়া ইঁহার ভুলটা শুধু ভুল, কিন্তু ওঁদের ভুলগুলা ভুল ত বটেই এবং আরো কিছু ! যাহারা সোজা পথে চলিয়া ভুল করে, তাদের ভুল একদিন আপনিই শুধরাইয়া যায়, কিন্তু যাহারা বাঁকা পথে চলিতে চায়, অথচ পথ চেনে না, তাদের ভবিষ্যৎ অধিকতর বিপজ্জনক হইয়া উঠিতে থাকে। শ্রীমতী নিরুপমার ‘অন্নপূর্ণার মন্দির’ পড়িবার সময় দুই-একটা সোজা ভুল চোখে ঠেকিয়াছিল, কিন্তু এখন আর তাহা মনে করিতে পারিতেছি না। তবে, একটা মনে আছে, দৃষ্টান্তের মত উল্লেখ করিতেছি। একস্থানে ‘সন্তরণ মূঢ়ের ন্যায়’ না বলিয়া ‘সন্তরণহীন মূঢ়ের ন্যায়’ বলিয়াছেন।
এটা বুঝিবার ভুল। বঙ্কিমবাবু যেমন কৃষ্ণকান্তের উইলের গোড়াতেই ‘ইহলোকান্ত’ না বলিয়া একাধিক বার ‘পরলোকান্তে’ বলিয়াছেন—তেমনি। কিন্তু, এটা যদি রবিবাবুর অনুকরণ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে অন্যায় করা হইয়াছে। তিনি ‘সন্তরণ মূঢ় রমেশ সঙ্গীতের হাঁটুজলে’ ইত্যাদি বলিয়াছেন, ‘সন্তরণহীন’ বলেন নাই। যাহা হউক, এটা ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। কিন্তু ধর্তব্যের মধ্যে সেইটা নিশ্চয়ই, যেটা না জানা সত্ত্বেও লেখা হইয়াছে। যেখানে সতী আফিং এবং বেলেডোনা দু-ই খাইয়াছে। একটা বিষ, আর একটা প্রতিষেধক। বেলেডোনা বিষে ডাক্তারেরা ‘মরফিন্’ ইনজেকট করেন। দুইটা বিষ একসঙ্গে সেবন করিলে দুর্ভাগা যে অনেক সময়ে শুধু মরে না, তা নয়, মরিলেও অত শীঘ্র, অত আরামে মমে না। অনেক বিলম্বে অনেক কষ্টে মরে। সেটা নিশ্চয়ই লেখিকার অভিপ্রায় ছিল না। তাছাড়া, দুর্ঘটনার আশঙ্কা যথেষ্ট ছিল। হয়ত, মরিতই না, হয়ত পোড়াইবার সময় চোখ চাহিয়া ফেলিত! যাহা হউক, যখন নির্বিঘ্নে কার্যোদ্ধার হইয়াছে, তখন আর আলোচনার প্রয়োজন নাই। কিন্তু বেলেডোনা যোগাড় করিবার জন্য মালিশের ঔষধ, ডাক্তার, ডাক্তারখানা, বাত ইত্যাদি অনেক অবান্তর কথার অবতারণা করিতে হইয়াছে। সুতরাং, একটুখানি জানিয়া লিখিলে আর এই বাজে মেহন্নতগুলা করিতে হইত না।
আর না। এইবার সমাপ্ত করি। অপ্রিয় কথা অনেক লিখিলাম। আশা করি, ইহাতে সুফল ফলিবে। আর যদি প্রচলিত নিয়মানুসারে লিখক-লেখিকারা এই বলিয়া সান্ত্বনা লাভ করিবার চেষ্টা করেন যে, সমালোচকেরা নিজেরা লিখিতে পারে না বলিয়াই হিংসা করিয়া গ্লানি করে, তাহা হইলে আমি নিরুপায়। কিন্তু সমালোচক মাত্রেই যে লিখিতে পারে না, এবং পারে না বলিয়াই দোষ দেখাইয়া বেড়ায়, এ কথাটার উপরেও তত আস্থা রাখা ঠিক নয়।
শ্রীঅনিলা দেবী ( ‘যমুনা’, ফাল্গুন ১৩১৯)
নূতন প্রোগ্রাম
শ্রীপরশুরাম
শরৎবাবুর রংপুর অভিভাষণের উত্তরে চরকা লইয়া কথা-কাটাকাটি হইয়া গেল বিস্তর, আজও তার শেষ হয় নাই। প্রথমে চরকা-ভক্তের দল প্রচার করিয়া দিলেন, তিনি মহাত্মাজীর টিকিতে চরকা বাঁধিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এতবড় একটা অমর্যাদাকর উক্তি অভিভাষণে ছিল না, কিন্তু তা বলিলে কি হয়,—ছিলই। না হইলে আর ভক্তের বেদনা প্রকাশের সুযোগ মিলিবে কি করিয়া? কিন্তু শরৎবাবু নিজে যখন নীরব, তখন আমার মতন একজন সাধারণ ব্যক্তির ওকালতি করিতে যাওয়া অনাবশ্যক। নিজের মাথায় টিকি নাই, কেহ যে ধরিয়া রাগ করিয়া বাঁধিয়া দিবে, সেও পারিবে না, সুতরাং এদিকে নিরাপদ। কিন্তু অভিভাষণে কেবল টিকিই ত ছিল না, চরকাও ছিল যে, অতএব বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্র ঢাকা হইতে দ্রুতবেগে গেলেন মানভূমে, এবং প্রতিবাদ করিলেন যুব-সমিতির সম্মিলনে। ঠিকই হইয়াছে, ওটা যুব-সমিতিরই ব্যাপার। তরুণ বৈজ্ঞানিক বুড়া সাহিত্যিকের তামাক খাওয়ার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি জানাইয়া ফিরিয়া আসিলেন, সকলে একজনকে ধন্য ধন্য এবং অপরকে ছি ছি করিতে লাগিল, তথাপি ভরসা হয় না যে, তিনি তিন কাল পার করিয়া দিয়া অবশেষে এই শেষ কালটাতেই তামাক ছাড়িবেন। অতঃপর শুরু হইয়া গেল প্রতিবাদের প্রতিবাদ, আবার তারও প্রতিবাদ। দুই-একটা কাগজ খুলিলে এখনও একটা-না-একটা চোখে পড়ে।
কিন্তু আমরা ভাবি, শরৎবাবুর অপরাধ হইল কিসে? তিনি বলিয়াছিলেন, বাঙলাদেশের লোকে চরকা গ্রহণ করে নাই। সুতরাং গ্রহণ না করার জন্য অপরাধ যদি থাকে, সে এ দেশের লোকের। খামকা তাঁহার উপর রাগ করিয়া লাভ কি? এ বিষয়ে আমার নিজেরও যৎকিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা আছে। স্বচক্ষে দেখিয়াছি ত এই বছর-আষ্টেক চরকা লইয়া লোকের সঙ্গে কি ধস্তাধস্তিটাই না হইল! কিন্তু প্রথম হইতেই মানুষে সেই যে ঘাড় বাঁকাইয়া রহিল, স্বরাজের লোভ, মহাত্মাজীর দোহাই, বন্দেমাতরমের দিব্যি, কোন কিছু দিয়াই সে বাঁকা ঘাড় আর সোজা করা গেল না, যে বা লইল, চরকার দাম দিল না; বক্তৃতার জোরে যাহাকে দলে আনা গেল, সে বিপদ ঘটাইল আরও বেশি। নব উৎসাহে কাজে মন দিয়া দিন দশ-পনেরো পরেই জোটপাকানো এক মুঠা সূতা আনিয়া হাজির করিল।
আষ্টেপৃষ্ঠে তাহাতে নামধাম-সমেত লেবেল আঁটা, অর্থাৎ গোলমালে ক্ষোয়া না যায়। কহিল, দিন ত মশাই একখানা প্রমাণ শাড়ি বুনে।
কর্মীরা কহিল—এতে কি কখনো শাড়ি হয়?
হয় না? আচ্ছা, শাড়িতে কাজ নেই, ধুতিই বুনে দিন, কিন্তু দেখবেন, বহর ছোট করে ফেলবেন না যেন।
কর্মীরা—এতে ধুতিও হবে না।
হবে না কিরকম? আচ্ছা ঝাড়া দশ হাত না হোক ন’হাত সাড়ে ন’হাত ত হবে? বেশ তাতেই চলবে। আচ্ছা চললুম।—এই বলিয়া সে চলিয়া যাইতে উদ্যত।
কর্মীরা প্রাণের দায়ে তখন চীৎকার করিয়া হাতমুখ নাড়িয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিত যে, এ ঢাকাই মসলিন নয়,—খদ্দর। এক মুঠো সূতার কাজ নয় মশাই, অন্ততঃ এক ধামা সূতার দরকার।
কিন্তু এ ত গেল বাহিরের লোকের কথা। কিন্তু তাই বলিয়া কর্মীদের উৎসাহ-উদ্যম অথবা খদ্দর-নিষ্ঠার লেশমাত্র অভাব ছিল, তাহা বলিতে পারিব না। প্রথম যুগের মোটা খদ্দরের ভারের উপরেই প্রধানতঃ patriotism নির্ভর করিত।
সুভাষচন্দ্রের কথা মনে পড়ে। তিনি পরিয়া আসিতেন দিশি সামিয়ানা তৈরির কাপড় মাঝখানে সেলাই করিয়া। সমবেত প্রশংসার মৃদু গুঞ্জনে সভা মুখরিত হইয়া উঠিত, এবং সেই পরিধেয় বস্ত্রের কর্কশতা, দৃঢ়তা, স্থায়িত্ব ও ওজনের গুরুত্ব কল্পনা করিয়া কিরণশঙ্কর প্রমুখ ভক্তবৃন্দের দুই চক্ষু ভাবাবেশে অশ্রুসজল হইয়া উঠিত।
কিন্তু সামিয়ানার কাপড়ে কুলাইল না, আসিল লয়ন-ক্লথের যুগ। সেদিন আসল ও নকল কর্মী এক আঁচড়ে চিনা গেল। যথা, অনিলবরণ—দীর্ঘ শুভ্রদেহের লয়নটুকু মাত্র ঢাকিয়া যখন কাঠের জুতা পায়ে খটাখট শব্দে সভায় প্রবেশ করিতেন, তখন শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে উপস্থিত সকলেই চোখ মুদিয়া অধোবদনে থাকিত। এবং তিনি সুখাসীন না হওয়া পর্যন্ত কেহ চোখ তুলিয়া চাহিতে সাহস করিত না। সে কি দিন! “My only answer is Charka” অধোমুখে বসিয়া সকলেই এই মহাকাব্য মনে মনে জপ করিয়া ভাবিত, ইংরাজের আর রক্ষা নাই, ল্যাঙ্কাশায়ারে লালবাতি জ্বালিয়া ব্যাটারা মরিল বলিয়া। আজ অনিলবরণ বোধ করি যোগাশ্রমে ধ্যানে বসিয়া ইহারই প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন।
সেদিন ফরেন ক্লথ মানেই ছিল মিল-ক্লথ। তা সে যেখানেরই তৈরি হউক না কেন। সেদিন অপবিত্র মিল-ক্লথ পরিব না প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি কোনও স্বদেশভক্ত দিগম্বর মূর্তিতেও কংগ্রেসে প্রবেশ করিত, ৩১শে ডিসেম্বরের মুখ চাহিয়া কাহারও সাধ্য ছিল না কথাটি বলে।
রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন—The programme of the Charka is so utterly childish that it makes one despair to see the whole country deluded by it.
সেদিন কেন যে কবি এতবড় দুঃখ করিয়াছিলেন, আজ তাহার কারণ বুঝা যায়। কিন্তু এখনও এ মোহ সকলের কাটে নাই,—প্রায় তেমনি অক্ষয় হইয়াই আছে, তাহারও বহু নিদর্শন বক্তৃতায়, প্রবন্ধে, খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় দেখা যায়। কিন্তু ইহার আর উপায় নাই। কারণ, ব্যক্তিগত ভক্তি অন্ধ হইয়া গেলে কোথাও তাহার আর সীমা থাকে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাঙলায় খদ্দরের একজন বড় আড়তদারের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। আশ্রম তৈরি হইতে আরম্ভ করিয়া ছাগ-দুগ্ধ পান করা পর্যন্ত, তিনি সমস্তই গ্রহণ করিয়াছেন—তেমনি টিকি, তেমনি কাপড় পরা, তেমনি চাদর গায়ে দেওয়া, তেমনি হাঁটু মুড়িয়া বসা, তেমনি মাটির দিকে চাহিয়া মৃদু মধুর বাক্যালাপ—সমস্ত। কিন্তু ইহাতেও নাকি পূজার উপচার সম্পূর্ণ হয় নাই, ষোলকলায় হৃদয় ভরে নাই; উপেন্দ্রনাথ বলেন, এবার নাকি তিনি সম্মুখের দাঁতগুলি তুলিয়া ফেলিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। বাস্তবিক, এ অনুরাগ অতুলনীয়, মনে হয় যেন বৈজ্ঞানিক প্রফুল্ল ঘোষকেও ইনি হার মানাইয়াছেন।
কিন্তু এ হইল উচ্চাঙ্গের সাধন-পদ্ধতি, সকলের অধিকার জন্মে না। এ পর্যায়ে যাঁহারা উঠিতে পারেন নাই, একটু নীচের ধাপে আছেন, তাঁহাদেরও চরকা-যুক্তি যথেষ্টই হৃদয়গ্রাহী। একটা কথা বারংবার বলা হয়, চরকা কাটিলে আত্মনির্ভরতা জন্মে, কিন্তু এ জিনিসটা যে কি, কেন জন্মায়, এবং চরকা ঘুরাইয়া বাহুবল বৃদ্ধি কিংবা আর কোন গূঢ়তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা বারংবার বলা সত্ত্বেও ঠিক বুঝা যায় না। তবে এ কথা স্বীকার করি, আত্মনির্ভরতার ধারণা সকলেরই এক নয়। যেমন আমাদের পরাণ একবার আত্মনির্ভরতার বক্তৃতা দিয়া বক্তব্য সুপরিস্ফুট করার উদ্দেশ্যে উপসংহারে concrete উদাহরণ দিয়া বলিয়াছিলেন,—“মনে কর তুমি গাছে চড়িয়া পড়িয়া গেলে।
কিন্তু পড়িতে পড়িতে তুমি হঠাৎ যদি একটি ডাল ধরিয়া ফেলিতে পার, তবেই জানিবে, তোমার আত্মনির্ভরতা (Self-help) শিক্ষা হইয়াছে,—তুমি স্বাবলম্বী হইয়াছ।”
অবশ্য এরূপ হইলে বিবাদের হেতু নাই। কিন্তু এ ত গেল সূক্ষ্ম দিক। ইহার স্থূল দিকের আলোচনাটাই বেশী দরকারী। বিশেষজ্ঞ বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের উক্তির নজির দিয়া প্রায়ই বলা হয়, অবসরকালে দু-চার ঘণ্টা করিয়া প্রত্যহ চরকা কাটিলে মাসিক আট আনা দশ আনা বারো আনা আয় বাড়ে। গরীব দেশে এই ঢের। অবশ্য গরীব শব্দটা অনাপেক্ষিক বস্তু নয়, একটা তুলনাত্মক শব্দ। Economics-এ marginal necessity-র উল্লেখ আছে, সে যে দেশের শাস্ত্র, সেই দেশের উপলব্ধির ব্যাপার। আমাদের এ দেশের গরীব কথাটার মানে আমরা সবাই বুঝি, এ লইয়া তর্ক করি না, কিন্তু এই দৈনিক এক পয়সা দেড় পয়সার আয়-বৃদ্ধিতে চাষারা খাইয়া পরিয়া পুরুষ্টু হইয়া কি করিয়া যে ইংরাজ তাড়াইয়া স্বরাজ আনিবে, ইহাই বুঝা কঠিন।
অনিলবরণ বলেন, কোথায় চরকা, কোথায় তুলো, কোথায় ধুনুরি, এত হাঙ্গামা না করিয়া অবসরমত দু’মুঠা ঘাস ছিঁড়িলেও ত মাসিক দশবার আনা অর্থাৎ দিনে এক পয়সা দেড় পয়সা রোজগার হয়। তিনি আরও বলেন, ইহাতে অন্য উপকারও আছে। এ. আই. সি. সি.-র একটা মিটিং ডাকিয়া franchise করিয়া দিলে লিডারদের তখন ঘাস ছিঁড়িতে পাড়াগাঁয়ে আসিতে হইবে। কারণ, শহরে ঘাস মেলে না। অতএব এরূপ মেলামেশায় পল্লী-সংগঠনের কাজটাও দ্রুত আগাইয়া যাইবে। অন্ততঃ শহরের মধ্যে মোটর হাঁকাইয়া লোক চাপা দিয়া মারার দুষ্কর্মটা কিছু কম হওয়ারই সম্ভাবনা।
আমি বলি, অনিলবরণের প্রস্তাবটিকে “due consideration” দেওয়া উচিত। রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরিয়াছেন, তিনি হয়ত শুনিয়া বলিবেন, ইহাও utterly childish, কিন্তু আমরা বলিব, কবিদের বুদ্ধি-সুদ্ধি নাই,—সুতরাং তাঁহার কথা শোনা চলিবে না। বিশেষতঃ বার মাসের মধ্যে তের মাস থাকেন তিনি বিলাতে, দেশের আবহাওয়া তিনি জানেন কতটুকু? চরকা-বিশ্বাসী অহিংসকেরা হিংস্র অবিশ্বাসীদের ধিক্কার দিয়া প্রায়ই বলিয়া থাকেন, তোমরা চরকা-কাটার মত সোজা কাজটাই ধৈর্য ধরিয়া করিতে পার না, আর তোমরা করবে দেশোদ্ধার? ছি ছি, তোমাদের গলায় দড়ি!
শুনিয়া ইহারা ম্রিয়মাণ হইয়া যায়। হয়ত কেহ কেহ ভাবে, হবেও বা। চরকা কাটিতেই যখন পারিলাম না, তখন আমাদের দ্বারা আর কি হইবে? কিন্তু আমি বলি, হতাশ হইবার কারণ নাই। অনিলবরণের কর্ম-পদ্ধতি অন্ততঃ বছরখানেক trial দিয়া দেখা উচিত। কারণ আরও সহজ। চরকা কিনিতে হইবে না, শিখিতে হইবে না, তুলার চাষ করিতে হইবে না, বাজারের শরণাপন্ন হইতে হইবে না;—কোনও মুশকিল নাই। আর পদ্মার চর হইলে ত কথাই নাই, ছিঁড়িতেও হইবে না, ধরামাত্রেই খুশ্ করিয়া উপড়াইয়া আসিবে। স্বরাজ মুঠার মধ্যে।
কিন্তু অনিলবরণ বলিয়াছেন, আস্থাহীন হইলে চলিবে না। আপাতদৃষ্টিতে এই প্রথায় যত ছেলেমানুষী দেখাক, যুক্তি যত উলটা কথাই বলুক, তথাপি বিশ্বাস করিতে হইবে।
এক বৎসরে Dominion Status অবশ্যম্ভাবী! হইবেই হইবে। যদি না হয়? সে লোকের অপরাধ, প্রোগ্রামের নয়। এবং তখন অনায়াসে বলা চলিবে, এত সহজ কর্ম-পদ্ধতি যে দেশের লোক নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করিয়া সফল করিতে পারিল না, তাহাদের দিয়া কোনও কালেই কিছুই হইবে না। আসল জিনিস বিশ্বাস ও নিষ্ঠা। একটার যখন সুবিধা হইল না, তখন আর একটা লওয়া কর্তব্য। এমনি করিয়া চেষ্টা করিতে করিতেই একদিন খাঁটি প্রোগ্রামটি ধরা পড়িবে। পড়িবেই পড়িবে। জয় হোক অনিলবরণের! কত সস্তায় স্বরাজের রাস্তা বাত্লে দিলেন।
নিখিল-ভারত-কাটুনি-সঙ্ঘ খবর দিতেছেন, বিশ লাখ টাকার চরকা কিনিয়া বাইশ লাখ টাকার খাদি প্রস্তুত হইয়াছে। উৎসব লাগিয়া গেল, সবাই কহিল—আর চিন্তা নাই, বিদেশী কাপড় দূর হইল বলিয়া। কলিকাতার বড় কংগ্রেস আসন্নপ্রায়; সুভাষচন্দ্র বলিলেন, খবরদার! কলের তৈরি দেশী একগাছি সূতাও যেন একজিবিশনে না ঢোকে। এ ঢুকিলে আর উনি ঢুকিবেন না।
নলিনীরঞ্জন বিষয়ী মানুষ, কত ধানে কত চাল হয় খবর রাখা তাঁর পেশা, কপালে চোখ তুলিয়া বলিলেন, সে কি কথা! বিদেশী কাপড় বয়কট করার যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তোমার এই বাইশ লাখ দিয়া সত্তর-আশি ক্রোড়ের ধাক্কা সামলাইবে কেন?
সেইন-গোপ্তা সাহেব বীরদর্পে বলিলেন, আমার ঐ খদ্দর এক শ’ টুকরা করিয়া লেংটি পরিব।
নলিনীরঞ্জন কহিলেন, সে জানি, কিন্তু এক শ’ টুকরা কেন, উহার একগাছি করিয়া সূতা ভাগ করিয়া দিলেও যে ভাগে কুলাইবে না।
সুভাষ বলিলেন, বস্ত্র বয়কট পরে হইবে, আপাততঃ মহাত্মাজীর বয়কট সহিবে না।
কিরণশঙ্কর কহিলেন, ঠিক, ঠিক।
মহাত্মা আসিলেন, লোকমুখে খবর লইয়া দেশে ফিরিয়া certificate পাঠাইয়া দিলেন, ‘ফিলিস সরকাস’ মন্দ জমে নাই।
নেতারা টুঁ শব্দটি করিলেন না, পাছে রাগ করিয়া তিনি স্বরাজের চাবি-কাঠিটি আটকাইয়া রাখেন! বাঙলাদেশের যেখানে যত আশ্রম ছিল, তাহার তপস্বীরা বগল বাজাইয়া নাচিতে লাগিল,—কেমন! কর একজিবিশন!
আমরা বাইরের লোকেরা ভাবি, complete independence বটে! তাই Dominion Status-এ এদের মন উঠে না। আরও একটা কথা ভাবি, এ ভালই হইয়াছে যে দেশবন্ধু স্বর্গে গিয়াছেন। ‘ফিলিস সরকাসে’র বিবরণ Young India-র পাতায় তাঁহাকে চোখে দেখিতে হয় নাই।
শুনিয়াছি, জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসে এবার নেহেরু-রিপোর্ট পাশ হইয়াছে। বহুবিধ ছলচাতুরি পূর্বক সেই আরজি অবশেষে বিলাতী পার্লামেন্টে পেশ করা হইয়াছে। আশা ত ছিলই না, তবে সে দেশের পার্লামেন্ট নাকি এবার মেয়েদের হুকুম-মত তৈরি; সুতরাং এখন তাহারাই একপ্রকার ভারতের ভাগ্যবিধাতা। প্রবাদ, মেয়েরা দয়াময়ী, এবার তারা যদি এ দেশের দুর্ভাগা পুরুষদের কিছু দয়া করে। আমেন! ইতি
বর্তমান রাজনৈতিক প্রসঙ্গ
কংগ্রেস ভুল করেছে—এমনি একটা চীৎকার কিছুদিন ধরে শুনছি। এই কোলাহলের মধ্যে সত্য বস্তু আছে কতটুকু, তার বিচার কিন্তু হয়নি।
নিজে আমি কোনদিনই হঠাৎ কোন বিষয়ে ধারণা গড়ে নিতে পারিনে। যারা জোর গলায় প্রচার করে যে, তাদের দাবীই প্রবল, সহজে তাদের কথাও আমি স্বীকার করে নিইনে। তাই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এই যুক্তিহীন নিন্দাপ্রচার আমার পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন।
যিনি এই নব-আন্দোলনের পুরোভাগে রয়েছেন, তাঁকে আমি একনিষ্ঠ প্রবীণ কর্মী হিসেবে শ্রদ্ধা করি; দেশের রাজনৈতিক সাধনার ইতিহাসে দান তাঁর কম বলেও মনে করিনে। কিন্তু দেশের প্রতি দুঃখবোধ তাঁর কংগ্রেসের চেয়েও বেশী, এ কথা প্রমাণের জন্য নূতন কোন দল গঠনের প্রয়োজন বোধ করি ছিল না। কংগ্রেস দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কংগ্রেস চিরকাল লড়াই করে এসেছে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে। আজ তাকে ছোট প্রমাণ করবার চেষ্টায় ব্যক্তিগত গৌরব কারও কিছুমাত্র বেড়েছে কিনা জানিনে, কিন্তু দেশের গৌরব বুঝি এতটুকুও বাড়েনি।
দেশসেবা জিনিসটা যতদিন ধর্ম হয়ে না দাঁড়ায়, ততদিন তার মধ্যে খানিকটা ফাঁকি থেকে যায়। এ কথা আমি প্রতিদিন মর্মে মর্মে অনুভব করি। আবার ধর্ম যখন দেশের মাথা ছাড়িয়ে ওঠে, তখনও ঘটে বিপদ। মহাত্মা জানেন এবং ওয়ার্কিং কমিটিও জানেন যে, ভুল তাঁরা করেন নি। মালব্যজী এবং অ্যানের বিরুদ্ধাচরণও মহাত্মাকে বিচলিত করেনি।
সুতরাং তিনি যদি কংগ্রেসের সম্পর্ক ত্যাগই করেন, তার সঙ্গে এ গোলযোগের কোন সম্বন্ধ থাকবে না। তাঁর আসল ভয় সোশিয়েলিজম্কে। তাঁকে ঘিরে রয়েছেন ধনিকরা, ব্যবসায়ীরা। সমাজতান্ত্রিকদের তিনি গ্রহণ করবেন কি করে? এইখানে মহাত্মার দুর্বলতা অস্বীকার করা চলে না।
একটা কথা আমি জানি যে, বাঙলাদেশের মুসলমানরাও ‘জয়েন্ট ইলেক্টোরেট’ চাইতে শুরু করেছেন। তা না হলে গলদ কোথায়, তা তাঁরা ভাল করেই জানেন। এ কথা ভুললে চলবে না যে, অধিকাংশ ধনী মুসলমানই নায়েব, গোমস্তা, উকিল, ডাক্তার হিসেবে স্বজাতির চেয়ে হিন্দুদের বিশ্বাস করেন বেশী। সঙ্গে সঙ্গে এও আমি বলি যে, প্রত্যেক হিন্দুই মনেপ্রাণে ন্যাশন্যালিস্ট। ধর্মবিশ্বাসেও তারা কারও হতে ছোট নয়। তাদের বেদ, তাদের উপনিষৎ, বহু মানুষের বহু তপস্যার ফল। তপস্যার মানেই হলো চিন্তা। বহুজনের বহুতর চিন্তার ফলে যে ধর্ম গড়ে উঠেছে, আইন-সভায় গুটিকতক আসন কম হবার আশঙ্কায়, তাকে সর্বনাশের ভয় দেখাবার প্রয়োজন বোধ করি ছিল না। (‘ নাগরিক,’ শারদীয় সংখ্যা, ১৩৪১).
বর্তমান হিন্দু-মুসলমান সমস্যা
কোন একটা কথা বহু লোকে মিলিয়া বহু আস্ফালন করিয়া বলিতে থাকিলেই কেবল বলার জোরেই তাহা সত্য হইয়া উঠে না। অথচ এই সম্মিলিত প্রবল কণ্ঠস্বরের একটা শক্তি আছে এবং মোহও কম নাই। চারিদিক গমগম করিতে থাকে—এবং এই বাষ্পাচ্ছন্ন আকাশের নীচে দুই কানের মধ্যে নিরন্তর যাহা প্রবেশ করে, মানুষ অভিভূতের মত তাহাকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া বসে। Propaganda বস্তুতঃ এই-ই। বিগত মহাযুদ্ধের দিনে পরস্পরের গলা কাটিয়া বেড়ানই যে মানুষের একমাত্র ধর্ম ও কর্তব্য, এই অসত্যকে সত্য বলিয়া যে দুই পক্ষের লোকেই মানিয়া লইয়াছিল, সে ত কেবল অনেক কলম এবং অনেক গলার সমবেত চীৎকারের ফলেই। যে দুই-একজন প্রতিবাদ করিতে গিয়াছিল, আসল কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের লাঞ্ছনা ও নির্যাতনের অবধি ছিল না।
কিন্তু আজ আর সেদিন নাই। আজ অপরিসীম বেদনা ও দুঃখ ভোগের ভিতর দিয়া মানুষের চৈতন্য হইয়াছে যে, সত্য বস্তু সেদিন অনেকের অনেক বলার মধ্যেই ছিল না।
বছর-কয়েক পূর্বে, মহাত্মার অহিংস অসহযোগের যুগে এমনি একটা কথা এদেশে বহু নেতায় মিলিয়া তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, হিন্দু-মুসলিম মিলন চাই-ই। চাই শুধু কেবল জিনিসটা ভাল বলিয়া নয়, চাই-ই এইজন্য যে, এ না হইলে স্বরাজ বল, স্বাধীনতা বল, তাহার কল্পনা করাও পাগলামি। কেন পাগলামি এ কথা যদি কেহ তখন জিজ্ঞাসা করিত, নেতৃবৃন্দেরা কি জবাব দিতেন তাঁহারাই জানেন, কিন্তু লেখায় বক্তৃতায় ও চীৎকারের বিস্তারে কথাটা এমনি বিপুলায়তন ও স্বতঃসিদ্ধ সত্য হইয়া গেল যে, এক পাগলা ছাড়া আর এত বড় পাগলামি করিবার দুঃসাহস কাহারও রহিল না।
তার পরে এই মিলন-ছায়াবাজীর রোশনাই যোগাইতেই হিন্দুর প্রাণান্ত হইল। সময় এবং শক্তি কত যে বিফলে গেল তাহার ত হিসাবও নাই। ইহারই ফলে মহাত্মাজীর খিলাফৎ-আন্দোলন, ইহারই ফলে দেশবন্ধুর প্যাক্ট। অথচ এতবড় দুটা ভুয়া জিনিসও ভারতের রাষ্ট্রনীতিক ক্ষেত্রে কম আছে। প্যাক্টের তবু বা কতক অর্থ বুঝা যায়; কারণ কল্যাণের হউক, অকল্যাণের হউক, সময়-মত একটা ছাড়রফা করিয়া কাউন্সিল-ঘরে বাঙলা সরকারকে পরাজিত করিবার একটা উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু খিলাফৎ-আন্দোলন হিন্দুর পক্ষে শুধু অর্থহীন নয়, অসত্য।
কোন মিথ্যাকেই অবলম্বন করিয়া জয়ী হওয়া যায় না। এবং যে মিথ্যার জগদ্দল পাথর গলায় বাঁধিয়া এত বড় অসহযোগ-আন্দোলন শেষ পর্যন্ত রসাতলে গেল, সে এই খিলাফৎ। স্বরাজ চাই, বিদেশীর শাসন-পাশ হইতে মুক্তি চাই, ভারতবাসীর এই দাবীর বিরুদ্ধে ইংরাজ হয়ত একটা যুক্তি খাড়া করিতে পারে, কিন্তু বিশ্বের দরবারে তাহা টিকে না। পাই বা না পাই, এই জন্মগত অধিকারের জন্য লড়াই করায় পুণ্য আছে, প্রাণপাত হইলে অন্তে স্বর্গবাস হয়। এই সত্যকে অস্বীকার করিতে পারে জগতে এমন কেহ নাই। কিন্তু খিলাফৎ চাই—এ কোন্ কথা? যে-দেশের সহিত ভারতের সংস্রব নাই, যে-দেশের মানুষে কি খায়, কি পরে, কি রকম তাদের চেহারা, কিছুই জানি না, সেই দেশ পূর্বে তুর্কীর শাসনাধীন ছিল, এখন যদিচ, তুর্কী লড়াইয়ে হারিয়াছে, তথাপি সুলতানকে তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হউক, কারণ, পরাধীন ভারতীয় মুসলমান-সমাজ আবদার ধরিয়াছে। এ কোন্ সঙ্গ-ত প্রার্থনা? আসলে ইহাও একটা প্যাক্ট। ঘুষের ব্যাপার। যেহেতু আমরা স্বরাজ চাই, এবং তোমরা চাও খিলাফৎ—অতএব এস, একত্র হইয়া আমরা খিলাফতের জন্য মাথা খুঁড়ি এবং তোমরা স্বরাজের জন্য তাল ঠুকিয়া অভিনয় শুরু কর। কিন্তু এদিকে বৃটিশ গভর্নমেন্ট কর্ণপাত করিল না, এবং ওদিকে যাহার জন্য খিলাফৎ সেই খলিফাকেই তুর্কীরা দেশ হইতে বাহির করিয়া দিল। সুতরাং এইরূপে খিলাফৎ-আন্দোলন যখন নিতান্তই অসার ও অর্থহীন হইয়া পড়িল, তখন নিজের শূন্যগর্ভতায় সে শুধু নিজেই মরিল না, ভারতের স্বরাজ-আন্দোলনেরও প্রাণবধ করিয়া গেল। বস্তুতঃ এমন ঘুষ দিয়া, প্রলোভন দেখাইয়া, পিঠ চাপড়াইয়া কি স্বদেশের মুক্তি-সংগ্রামে লোক ভরতি করা যায়, না করিলেই বিজয় লাভ হয়? হয় না, এবং কোনদিন হইবে বলিয়াও মনে করি না।
এই ব্যাপারে সব চেয়ে বেশী খাটিয়াছিলেন মহাত্মাজী নিজে। এতখানি আশাও বোধ করি কেহ করে নাই, এতবড় প্রতারিতও বোধ করি কেহ হয় নাই। সেকালে বড় বড় মুসলিম পাণ্ডাদের কেহ-বা হইয়াছিলেন তাঁহার দক্ষিণ হস্ত, কেহ-বা বাম হস্ত, কেহ-বা চক্ষু-কর্ণ, কেহ-বা আর কিছু,—হায়রে! এত বড় তামাশার ব্যাপার কি আর কোথাও অনুষ্ঠিত হইয়াছে! পরিশেষে হিন্দু-মুসলমান-মিলনের শেষ চেষ্টা করিলেন তিনি দিল্লীতে—দীর্ঘ একুশ দিন উপবাস করিয়া। ধর্মপ্রাণ সরলচিত্ত সাধু মানুষ তিনি, বোধ হয় ভাবিয়াছিলেন, এতখানি যন্ত্রণা দেখিয়াও কি তাহাদের দয়া হইবে না! সে-যাত্রা কোনমতে প্রাণটা তাঁহার টিকিয়া গেল।
ভ্রাতার অধিক, সর্বাপেক্ষা প্রিয় মিঃ মহম্মদ আলিই বিচলিত হইলেন সবচেয়ে বেশি। তাঁহার চোখের উপরেই সমস্ত ঘটিয়াছিল,—অশ্রুপাত করিয়া কহিলেন, আহা! বড় ভাল লোক এই মহাত্মাজীটি। ইঁহার সত্যকার উপকার কিছু করাই চাই। অতএব আগে যাই মক্কায়, গিয়া পীরের সিন্নি দিই, পরে ফিরিয়া আসিয়া কলমা পড়াইয়া কাফের-ধর্ম ত্যাগ করাইয়া তবে ছাড়িব।
শুনিয়া মহাত্মা কহিলেন, পৃথিবী দ্বিধা হও।
বস্তুতঃ, মুসলমান যদি কখনও বলে—হিন্দুর সহিত মিলন করিতে চাই, সে যে ছলনা ছাড়া আর কি হইতে পারে, ভাবিয়া পাওয়া কঠিন।
একদিন মুসলমান লুণ্ঠনের জন্যই ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল, রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আসে নাই। সেদিন কেবল লুঠ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মন্দির ধ্বংস করিয়াছে, প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে, নারীর সতীত্ব হানি করিয়াছে, বস্তুতঃ অপরের ধর্ম ও মনুষ্যত্বের উপরে যতখানি আঘাত ও অপমান করা যায়, কোথাও কোন সঙ্কোচ মানে নাই।
দেশের রাজা হইয়াও তাহারা এই জঘন্য প্রবৃত্তির হাত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। ঔরঙ্গজেব প্রভৃতি নামজাদা সম্রাটের কথা ছাড়িয়া দিয়াও যে আকবর বাদশাহের উদার বলিয়া এত খ্যাতি ছিল, তিনিও কসুর করেন নাই। আজ মনে হয়, এ সংস্কার উহাদের মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে। পাবনার বীভৎস ব্যাপারে অনেককেই বলিতে শুনি, পশ্চিম হইতে মুসলমান মোল্লারা আসিয়া নিরীহ ও অশিক্ষিত মুসলমান প্রজাদের উত্তেজিত করিয়া এই দুষ্কার্য করিয়াছে। কিন্তু এমনিই যদি পশ্চিম হইতে হিন্দু পুরোহিতের দল আসিয়া, কোন হিন্দুপ্রধান স্থানে এমনি নিরীহ ও নিরক্ষর চাষাভূষাদের এই বলিয়া উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করেন যে নিরপরাধ মুসলমান প্রতিবেশীদের ঘরদোরে আগুন ধরাইয়া সম্পত্তি লুঠ করিয়া মেয়েদের অপমান অমর্যাদা করিতে হইবে, তাহা হইলে সেই-সব নিরক্ষর হিন্দু কৃষকের দল উহাদের পাগল বলিয়া গ্রাম হইতে দূর করিয়া দিতে একমুহূর্ত ইতস্ততঃ করিবে না।
কিন্তু, কেন এরূপ হয়? ইহা কি শুধু কেবল অশিক্ষারই ফল? শিক্ষা মানে যদি লেখাপড়া জানা হয়, তাহা হইলে চাষী-মজুরের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানে বেশি তারতম্য নাই। কিন্তু শিক্ষার তাৎপর্য যদি অন্তরের প্রসার ও হৃদয়ের কাল্চার হয়, তাহা হইলে বলিতেই হইবে উভয় সম্প্রদায়ের তুলনাই হয় না।
হিন্দুনারীহরণ ব্যাপারে সংবাদপত্রওয়ালারা প্রায়ই দেখি প্রশ্ন করেন, মুসলমান নেতারা নীরব কেন? তাঁহাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা যে পুনঃ পুনঃ এতবড় অপরাধ করিতেছে, তথাপি প্রতিবাদ করিতেছেন না কিসের জন্য? মুখ বুজিয়া নিঃশব্দে থাকার অর্থ কি? কিন্তু আমার ত মনে হয় অর্থ অতিশয় প্রাঞ্জল। তাঁহারা শুধু অতি বিনয়বশতঃই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারেন না, বাপু, আপত্তি করব কি, সময় এবং সুযোগ পেলে ও-কাজে আমরাও লেগে যেতে পারি।
মিলন হয় সমানে সমানে। শিক্ষা সমান করিয়া লইবার আশা আর যেই করুক আমি ত করি না। হাজার বৎসরে কুলায় নাই, আরও হাজার বৎসরে কুলাইবে না। এবং ইহাকেই মূলধন করিয়া যদি ইংরাজ তাড়াইতে হয় ত সে এখন থাক। মানুষের অন্য কাজ আছে। খিলাফৎ করিয়া, প্যাক্ট করিয়া, ডান ও বাঁ—দুই হাতে মুসলমানের পুচ্ছ চুলকাইয়া স্বরাজযুদ্ধে নামান যাইতে পারিবে, এ দুরাশা দুই-একজনার হয়ত ছিল, কিন্তু মনে মনে অধিকাংশেরই ছিল না। তাঁহারা ইহাই ভাবিতেন—দুঃখ-দুর্দশার মত শিক্ষক ত আর নাই, বিদেশী বুরোক্রেসির কাছে নিরন্তর লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া হয়ত তাহাদের চৈতন্য হইবে, হয়ত হিন্দুর সহিত কাঁধ মিলাইয়া স্বরাজরথে ঠেলা দিতে সম্মত হইবে। ভাবা অন্যায় নয়, শুধু ইহাই তাঁহারা ভাবিলেন না যে, লাঞ্ছনাবোধও শিক্ষাসাপেক্ষ। যে লাঞ্ছনার আগুনে স্বর্গীয় দেশবন্ধুর হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইত, আমার গায়ে তাহাতে আঁচটুকুও লাগে না। এবং তাহার চেয়েও বড় কথা এই যে, দুর্বলের প্রতি অত্যাচার করিতে যাহাদের বাধে না, সবলের পদলেহন করিতেও তাহাদের ঠিক ততখানিই বাধে না। সুতরাং, এ আকাশকুসুমের লোভে আত্মবঞ্চনা করি আমরা কিসের জন্য? হিন্দু-মুসলমান-মিলন একটা গালভরা শব্দ, যুগে যুগে এমন অনেক গালভরা বাক্যই উদ্ভাবিত হইয়াছে, কিন্তু ঐ গাল-ভরানোর অতিরিক্ত সে আর কোন কাজেই আসে নাই। এ মোহ আমাদিগকে ত্যাগ করিতেই হইবে। আজ বাঙলার মুসলমানকে এ কথা বলিয়া লজ্জা দিবার চেষ্টা বৃথা যে, সাতপুরুষ পূর্বে তোমরা হিন্দু ছিলে; সুতরাং রক্ত-সম্বন্ধে তোমরা আমাদের জ্ঞাতি। জ্ঞাতিবধে মহাপাপ, অতএব কিঞ্চিৎ করুণা কর। এমন করিয়া দয়াভিক্ষা ও মিলন-প্রয়াসের মত অগৌরবের বস্তু আমি ত আর দেখিতে পাই না। স্বদেশে-বিদেশে ক্রীশ্চান বন্ধু আমার অনেক আছেন।
কাহারও বা পিতামহ, কেহ-বা স্বয়ং ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু নিজে হইতে তাঁহারা নিজেদের ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় না দিলে বুঝিবার জো নাই যে, সর্বদিক দিয়া তাঁহারা আজও আমাদের ভাইবোন নয়। একজন মহিলাকে জানি, অল্প বয়সেই তিনি ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, এতবড় শ্রদ্ধার পাত্রীও জীবনে আমি কম দেখিয়াছি! আর মুসলমান? আমাদের একজন পাচক ব্রাহ্মণ ছিল। সে মুসলমানীর প্রেমে মজিয়া ধর্মত্যাগ করে। এক বৎসর পরে দেখা। তাহার নাম বদলাইয়াছে, পোশাক বদলাইয়াছে, প্রকৃতি বদলাইয়াছে, ভগবানের দেওয়া যে আকৃতি, সে পর্যন্ত এমনি বদলাইয়া গিয়াছে যে আর চিনিবার জো নাই। এবং এইটিই একমাত্র উদাহরণ নয়। বস্তির সহিত যাঁহারই অল্পবিস্তর ঘনিষ্ঠতা আছে,—এ কাজ যেখানে প্রতিনিয়তই ঘটিতেছে—তাঁহারই অপরিজ্ঞাত নয় যে এমনিই বটে! উগ্রতায় পর্যন্ত ইহারা বোধ হয় কোহাটের মুসলমানকেও লজ্জা দিতে পারে।
অতএব, হিন্দুর সমস্যা এ নয় যে, কি করিয়া এই অস্বাভাবিক মিলন সংঘটিত হইবে; হিন্দুর সমস্যা এই যে, কি করিয়া তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিবেন এবং হিন্দুধর্মাবলম্বী যে-কোন ব্যক্তিকেই ছোট জাতি বলিয়া অপমান করিবার দুর্মতি তাঁহাদের কেমন করিয়া এবং কবে যাইবে। আর সর্বাপেক্ষা বড় সমস্যা—হিন্দুর অন্তরের সত্য কেমন করিয়া তাহার প্রতিদিনের প্রকাশ্য আচরণে পুষ্পের মত বিকশিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইবে। যাহা ভাবি তাহা বলি না, যাহা বলি তাহা করি না, যাহা করি তাহা স্বীকার পাই না—আত্মার এত বড় দুর্গতি অব্যাহত থাকিতে সমাজগাত্রের অসংখ্য ছিদ্রপথ ভগবান স্বয়ং আসিয়াও রুদ্ধ করিতে পারিবেন না।
ইহাই সমস্যা এবং ইহাই কর্তব্য। হিন্দু-মুসলমানের মিলন হইল না বলিয়া বুক চাপড়াইয়া কাঁদিয়া বেড়ানই কাজ নয়। নিজেরা কান্না বন্ধ করিলেই তবে অন্য পক্ষ হইতে কাঁদিবার লোক পাওয়া যাইবে।
হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এ দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই। মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে,—এ দেশে চিত্ত তাহার নাই। যাহা নাই তাহার জন্য আক্ষেপ করিয়াই বা লাভ কি, এবং তাহাদের বিমুখ কর্ণের পিছু পিছু ভারতের জলবায়ু ও খানিকটা মাটির দোহাই পাড়িয়াই বা কি হইবে! আজ এই কথাটাই একান্ত করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন হইয়াছে যে, এ কাজ শুধু হিন্দুর,—আর কাহারও নয়।
মুসলমানের সংখ্যা গণনা করিয়া চঞ্চল হইবারও আবশ্যকতা নাই। সংখ্যাটাই সংসারে পরম সত্য নয়। ইহার চেয়েও বড় সত্য রহিয়াছে যাহা এক দুই তিন করিয়া মাথা-গণনার হিসাবটাকে হিসাবের মধ্যে গণ্য করে না।
হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি তাহা অনেকের কানেই হয়ত তিক্ত ঠেকিবে, কিন্তু সেজন্য চমকাইবারও প্রয়োজন নাই, আমাকে দেশদ্রোহী ভাবিবারও হেতু নাই। আমার বক্তব্য এ নয় যে, এই দুই প্রতিবেশী জাতির মধ্যে একটা সদ্ভাব ও প্রীতির বন্ধন ঘটিলে সে বস্তু আমার মনঃপূত হইবে না। আমার বক্তব্য এই যে, এ জিনিস যদি নাই-ই হয় এবং হওয়ারও যদি কোন কিনারা আপাততঃ চোখে না পড়ে ত এ লইয়া অহরহ আর্তনাদ করিয়া কোন সুবিধা হইবে না। আর না হইলেই যে সর্বনাশ হইয়া গেল এ মনোভাবেরও কোনও সার্থকতা নাই। অথচ, উপরে-নীচে, ডাহিনে-বামে, চারিদিক হইতে একই কথা বারংবার শুনিয়া ইহাকে এমনিই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছি যে জগতে ইহা ছাড়া যে আমাদের আর কোন গতি আছে, তাহা যেন আর ভাবিতেই পারি না। তাই করিতেছি কি? না, অত্যাচার ও অনাচারের বিবরণ সকল স্থান সংগ্রহ করিয়া এই কথাটাই কেবল বলিতেছি—তুমি এই আমাকে মারিলে, এই আমার দেবতার হাত-পা ভাঙ্গি-লে, এই আমার মন্দির ধ্বংস করিলে, এই আমার মহিলাকে হরণ করিলে,—এবং এ-সকল তোমার ভারী অন্যায়, ও ইহাতে আমরা যারপরনাই ব্যথিত হইয়া হাহাকার করিতেছি। এ-সকল তুমি না থামাইলে আমরা আর তিষ্ঠিতে পারি না। বাস্তবিক ইহার অধিক আমরা কি কিছু বলি, না করি? আমরা নিঃসংশয়ে স্থির করিয়াছি যে, যেমন করিয়াই হউক মিলন করিবার ভার আমাদের এবং অত্যাচার নিবারণ করিবার ভার তাহাদের। কিন্তু, বস্তুতঃ হওয়া উচিত ঠিক বিপরীত। অত্যাচার থামাইবার ভার গ্রহণ করা উচিত নিজেদের এবং হিন্দু-মুসলমান-মিলন বলিয়া যদি কিছু থাকে ত সে সম্পন্ন করিবার ভার দেওয়া উচিত মুসলমানদের ‘পরে।
কিন্তু দেশের মুক্তি হইবে কি করিয়া? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মুক্তি কি হয় গোঁজামিলে? মুক্তি অর্জনের ব্রতে হিন্দু যখন আপনাকে প্রস্তুত করিতে পারিবে, তখন লক্ষ্য করিবারও প্রয়োজন হইবে না, গোটা-কয়েক মুসলমান ইহাতে যোগ দিল কি না।
ভারতের মুক্তিতে ভারতীয় মুসলমানেরও মুক্তি মিলিতে পারে, এ সত্য তাহারা কোনদিনই অকপটে বিশ্বাস করিতে পারিবে না। পারিবে শুধু তখন যখন ধর্মের প্রতি মোহ তাহাদের কমিবে, যখন বুঝিবে যে-কোন ধর্মই হউক তাহার গোঁড়ামি লইয়া গর্ব করার মত এমন লজ্জাকর ব্যাপার, এতবড় বর্বরতা মানুষের আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু সে বুঝার এখনও অনেক বিলম্ব। এবং জগৎসুদ্ধ লোক মিলিয়া মুসলমানের শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে ইহাদের কোনদিন চোখ খুলিবে কিনা সন্দেহ। আর, দেশের মুক্তিসংগ্রামে কি দেশসুদ্ধ লোকেই কোমর বাঁধিয়া লাগে? না ইহা সম্ভব, না তাহার প্রয়োজন হয়। আমেরিকা যখন স্বাধীনতার জন্য লড়াই করিয়াছিল, তখন দেশের অর্ধেকের বেশি লোকে ত ইংরাজের পক্ষেই ছিল। আয়ার্লন্ডের মুক্তিযজ্ঞে কয়জনে যোগ দিয়াছিল? যে বলশেভিক গভর্নমেন্ট আজ রুশিয়ার শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতেছে, দেশের লোকসংখ্যার অনুপাতে সে ত এখনও শতকে একজনও পৌঁছে নাই। মানুষ ত গরু-ঘোড়া নয়, কেবলমাত্র ভিড়ের পরিমাণ দেখিয়াই সত্যাসত্য নির্ধারিত হয় না, হয় শুধু তাহার তপস্যার একাগ্রতার বিচার করিয়া। এই একাগ্র তপস্যার ভার রহিয়াছে দেশের ছেলেদের ‘পরে। হিন্দু-মুসলমান-মিলনের ফন্দি উদ্ভাবন করাও তাহার কাজ নহে, এবং যে-সকল প্রধান রাজনীতিবিদের দল এই ফন্দিটাকেই ভারতের একমাত্র ও অদ্বিতীয় বলিয়া চিৎকার করিয়া ফিরিতেছেন তাঁহাদের পিছনে জয়ধ্বনি করিয়া সময় নষ্ট করিয়া বেড়ানও তাহার কাজ নহে। জগতে অনেক বস্তু আছে যাহাকে ত্যাগ করিয়াই তবে পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলমান-মিলনও সেই জাতীয় বস্তু। মনে হয়, এ আশা নির্বিশেষে ত্যাগ করিয়া কাজে নামিতে পারিলেই হয়ত একদিন এই একান্ত দুষ্প্রাপ্য নিধির সাক্ষাৎ মিলিবে। কারণ, মিলন তখন শুধু কেবল একার চেষ্টাতেই ঘটিবে না, ঘটিবে উভয়ের আন্তরিক ও সমগ্র বাসনার ফলে।
বাংলা নাটক
তোমার প্রশ্ন—আমি নাটক লিখি না কেন? বোধ করি, তোমার এ জিজ্ঞাসা মনে এসেছে দুটো কারণে। প্রথম, নাট্যকার এবং অন্যান্য গ্রন্থকারের রচিত উপন্যাসের নাট্যরূপদাতা শ্রীযুক্ত যোগেশ চৌধুরী সম্প্রতি ‘বাতায়নে’ বাংলা নাটক সম্বন্ধে যে-মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তাকে তুমি সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিতে পারোনি এবং দ্বিতীয় হচ্ছে, তোমরা নিরন্তর যে-সমস্ত নাটকের অভিনয় দেখে থাকো, তাদের ভাব, ভাষা, চরিত্রগঠন ইত্যাদি বিচার করে দেখবার পর তোমাদের মনে এই কথা জেগেছে যে, শরৎচন্দ্র নাটক লিখলে হয়ত রঙ্গমঞ্চের চেহারায় একটু পরিবর্তন হতে পারে।
তোমার প্রশ্নের উত্তরে আমার প্রথম কথা এই যে, আমি নাটক লিখি না, তার কারণ হচ্ছে আমার অক্ষমতা। দ্বিতীয়, এই অক্ষমতাকে অস্বীকার করে যদিই বা নাটক লিখি, তা হলেও আমার মজুরি পোষাবে না। মনে করো না কথাটা টাকার দিক থেকেই শুধু বলছি। সংসারে ওটার প্রয়োজন, কিন্তু একমাত্র প্রয়োজন নয়, এ সত্য একদিনও ভুলিনে। উপন্যাস লিখলে মাসিক পত্রের সম্পাদক সাগ্রহে তা নিয়ে যাবেন, উপন্যাস ছাপাবার জন্যে পাব্লিশারের অভাব হবে না, অন্ততঃ হয়নি এত দিন এবং সেই উপন্যাস পড়বার লোকও পেয়ে এসেছি। গল্প লেখার ধারাটা আমি জানি। অন্ততঃ, শিখিয়ে দিন বলে কারও দ্বারস্থ হবার দুর্গতি আমার আজও ঘটেনি। কিন্তু নাটক? রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষই হচ্ছেন এর চরম হাইকোর্ট। মাথা নেড়ে যদি বলেন, এ জায়গায় আকশন (action) কম, দর্শকে নেবে না, কিংবা এই বই অচল, ত তাকে সচল করার কোন উপায় নেই। তাঁদের রায়ই এ সম্বন্ধে শেষ কথা। কারণ তাঁরা বিশেষজ্ঞ। টাকা-দেনেওয়ালা দর্শকের নাড়ী-নক্ষত্র তাঁদের জানা। সুতরাং এ বিপদের মধ্যে খামকা ঢুকে পড়তে মন আমার দ্বিধা বোধ করে।
নাটক হয়ত আমি লিখতে পারি। কারণ, নাটকের যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু—যা ভাল না হলে নাটকের প্রতিপাদ্য কিছুতেই দর্শকের অন্তরে গিয়ে পৌঁছয় না—সেই ডায়ালোগ লেখার অভ্যাস আমার আছে। কথাকে কেমন ভাবে বলতে হয়, কত সোজা করে বললে তা মনের ওপর গভীর হয়ে বসে, সে কৌশল জানিনে তা নয়। এ ছাড়া চরিত্র বা ঘটনা সৃষ্টির কথা যদি বল, সে কোশল জানিনে তা নয়।
এ ছাড়া চরিত্র বা ঘটনা সৃষ্টির কথা যদি বল, তাও পারি বলেই বিশ্বাস করি। নাটকে ঘটনা বা সিচুয়েশান সৃষ্টি করতে হয় চরিত্র-সৃষ্টির জন্যেই। চরিত্র-সৃষ্টি দু-রকমের হতে পারে :—এক হচ্ছে, প্রকাশ অর্থাৎ পাত্রপাত্রী যা, তাই ঘটনা-পরম্পরার সাহায্যে দর্শকের চোখের সুমুখে প্রকাশিত করা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে—চরিত্রের বিকাশ অর্থাৎ ঘটনা-পরম্পরার মধ্যে দিয়ে তার জীবনের পরিবর্তন দেখানো। সে ভালোর দিকেও হতে পারে, মন্দর দিকেও যেতে পারে। ধরো, একজন হয়ত বিশ বছর আগে উইল্সনের হোটেলে খেত, মিথ্যা কথা বলত এবং আরও অন্যান্য অকাজ করত। আজ সে ধার্মিক বৈষ্ণব—বঙ্কিমচন্দ্রের কথায়—পাতে মাছের ঝোল পড়লে হাত দিয়ে মুছে ফেলে দেয়। তবু এ হয়ত তার ভণ্ডামি নয়, সত্যিকারের আন্তরিক পরিবর্তন। হয়ত অনেকগুলো ঘটনার আবর্তে পড়ে পাঁচটা ভালো লোকের সংস্পর্শে এসে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আজ সে সত্যি করে বদলে গেছে। সুতরাং বিশ বছর আগে সে যা ছিল, তাও সত্যি এবং আজ সে যা হয়েছে, তাও সত্যি। কিন্তু যা-তা হলে ত হবে না,—বইয়ের মধ্যে দিয়ে লেখার মধ্যে দিয়ে পাঠক বা দর্শকের কাছে তাকে সত্যি করে তুলতে হবে। এমন যেন না তাঁদের মনে হয়, লেখার মধ্যে এ পরিবর্তনের হেতু খুঁজে মেলে না। কাজটা শক্ত। আর একটা কথা—উপন্যাসের মত নাটকের elasticity নেই; নাটককে একটা নির্দিষ্ট সময়ের বেশি এগুতে দেওয়া চলে না। ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে নাটককে দৃশ্যে বা অঙ্কে ভাগ করা,—তাও হয়ত চেষ্টা করলে দুঃসাধ্য হবে না। কিন্তু ভাবি, করে কি হবে? নাটক যে লিখব, তা অভিনয় করবে কে? শিক্ষিত বোঝদার অভিনেতা-অভিনেত্রী কৈ? নাটকের হিরোইন সাজবে, এমন একটিও অভিনেত্রী ত নজরে পাড়ে না। এমনি ধারা নানা কারণে সাহিত্যের এই দিকটায় পা বাড়াতে ইচ্ছে করে না। আশা করি একদিন বর্তমান রঙ্গালয়ের এই অভাবটা ঘুচবে, কিন্তু আমার তা হয়ত চোখে দেখে যেতে পারবো না। অবশ্য সত্যিকারের তাগিদ যদি আসে, কখনো হয়ত লিখতেও পারি। কিন্তু আশা বড় করিনে।
বাংলা বইয়ের দুঃখ
কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের বক্তৃতা শুনে আর কিছু না হোক অন্ততঃ একটি উপকার আমরা পেয়েছি। ইউরোপের নানা গ্রন্থাগার সম্বন্ধে তিনি যা বললেন হয়ত তার অনেক কথাই আমাদের মনে থাকবে না। কিন্তু আজ তাঁর বক্তৃতা শুনে আমাদের মনে জেগেছে একটা আকুলতা। ইউরোপের গ্রন্থাগারের অবস্থা যে-রকম উন্নত, সে-রকম অবস্থা যে আমাদের দেশে কবে হবে—তা কল্পনাও করা যায় না। তবে যেটুকু হওয়া সম্ভব, তার জন্যে আমাদের চেষ্টা করা উচিত। চারিদিক থেকে অভিযোগ ওঠে, আমাদের গ্রন্থাগারে ভাল বই নেই,—আছে কেবল বাজে নভেল। আমাদের লেখকেরা জ্ঞানগর্ভ বই লেখেন না। তাঁরা কেবল গল্প লেখেন। কিন্তু তাঁরা লিখবেন কোথা থেকে? এই অতিনিন্দিত গল্পলেখকদের দৈন্যের সীমা নেই। অনেকেরই উপন্যাসের হয়ত দ্বিতীয় সংস্করণ হয় না। যা বা লাভ হয় সে যে কার গর্ভে গিয়ে ঢোকে তা না বলাই ভাল। অনেকের হয়ত ধারণাই নেই যে, এই-সব লেখক-সম্প্রদায় কত নিঃস্ব, কত নিঃসহায়।
বিলাতে কিন্তু গল্পলেখকদের অবস্থা অন্যরকম। তারা ধনী। তাদের এক-একজনের আয় আমরা কল্পনা করতেও পারিনে। অল্প সময়ের মধ্যে তাদের পুস্তকের সংস্করণের পর সংস্করণ হয়। কারণ ও-দেশে অন্ততঃ সামাজিকতার দিক থেকেও লোক বই কেনে। কিন্তু আমাদের দেশে সে বালাই নেই। ও-দেশে বাড়িতে গ্রন্থাগার রাখা একটা আভিজাত্যের পরিচয়। শিক্ষিত সকলেরই বই কেনার অভ্যাস আছে। না কিনলে নিন্দে হয়,—হয়ত বা কর্তব্যেরও ত্রুটি ঘটে। আর অবস্থাপন্ন লোকদের ত কথাই নেই। তাঁদের প্রত্যেকেরই বাড়িতে এক-একটা বড় গ্রন্থাগার আছে। পড়ার লোক থাকুক বা না-থাকুক—গ্রন্থাগার রাখাই যেন একটা সামাজিক কর্তব্য। কিন্তু দুর্ভাগা জাত আমরা। আমাদের শিক্ষিতদের মধ্যেও পুস্তকের প্রচলন নেই।
অনেকে হয়ত মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে সমালোচনার ছলে শুধু গালিগালাজের উপকরণ সংগ্রহ করে নেন। যদি খোঁজ নেন ত দেখতে পাবেন, তাঁদের অনেকেই মূল বইখানা পর্যন্ত পড়েন নি। আমি নিজেও একজন সাহিত্য-ব্যবসায়ী। নানা জায়গা থেকে আমার ডাক আসে। অনেক বড়লোকের বাড়িতে আমি গেছি। খোঁজ নিয়ে দেখেছি, তাঁদের আছে সবই—নেই কেবল গ্রন্থাগার। বই কেনা তাঁদের অনেকের কাছেই অপব্যয় ছাড়া আর কিছুই নয়। যাঁদের বা একান্তই আছে, তাঁরা কয়েকখানা চকচকে বই বাইরের ঘরে সাজিয়ে রাখেন। কিন্তু বাংলা বই মোটেই কেনেন না।
তাই বাংলায়—যাকে আপনারা জ্ঞানগর্ভ বই বলছেন—সে হয় না, কারণ বিক্রি নেই। বিক্রি হয় না বলেই প্রকাশকেরা ছাপাতে চান না। তাঁরা বলেন, ও-সবের কোন চাহিদা নেই—নিয়ে এস গল্প। লোকে ভাবে, গল্পলেখাটা বড়ই সোজা। শুভানুধ্যায়ী পাড়ার লোকে যেমন অক্ষম আত্মীয়কে পরামর্শ দেয়—তোকে দিয়ে আর কিছু হবে না, যা তুই হোমিওপ্যাথি কর্গে যা। অথচ হোমিওপ্যাথির মত শক্ত কাজ খুব কমই আছে। এর কারণ হচ্ছে, যে জিনিসটা সকলের চেয়ে শক্ত, তাকেই অনেকে সবচেয়ে সহজ ধরে নেয়। ভগবান সম্বন্ধে কথা বলা যেমন দেখি, তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করতে কারও কখনো বিদ্যেবুদ্ধির অভাব ঘটে না।
গল্পলেখকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে কি হবে? টাকার অভাবে কত ভাল ভাল কল্পনা—কত বড় বড় প্রতিভা যে নষ্ট হয়ে যায়, তার খবর কে রাখে? যৌবনে আমার একটা কল্পনা ছিল,—একটা উচ্চাশা ছিল যে, ‘দ্বাদশ মূল্য’ নাম দিয়ে আমি একটা volume তৈরি করব। যেমন সত্যের মূল্য, মিথ্যার মূল্য, মৃত্যুর মূল্য, দুঃখের মূল্য, নরের মূল্য, নারীর মূল্য—এই রকম মূল্য-বিচার। তারই ভূমিকা হিসাবে তখনকার কালে ‘নারীর মূল্য’ লিখি। সেটা বহুদিন অপ্রকাশিত পড়ে থাকে।
পরে ‘যমুনা’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু সেই ‘দ্বাদশ মূল্য’ আর শেষ করতে পারিনি, তার কারণ—অভাব। আমার জমিদারি নেই, টাকা নেই, তখন এমন কি দু-বেলা ভাত জোটাবার পয়সা পর্যন্ত ছিল না; প্রকাশকেরা উপদেশ দিলেন, ও-সব চলবে না। তুমি যা তা করে তার চেয়ে দুটো গল্প লিখে দাও,—তবু হাজারখানেক কাটবে। আমাদের জাতির বৈশিষ্ট্যই বলুন, কিংবা দুর্ভাগ্যই বলুন, বই কিনে আমরা লেখকদের সাহায্য করি না। এমন কি যাঁদের সঙ্গতি আছে—তাঁরাও করেন না। বরং অভিযোগ করেন, গল্প লিখে হবে কি? অথচ আজ অন্তঃপুরে যেটুকু স্ত্রীশিক্ষার প্রচার হয়েচে, তা এই গল্পের ভেতর দিয়েই।
কত বড় বড় কবি উৎসাহের অভাবে নাম করতে পারেন নি। পরলোকগত সত্যেন দত্তর শোক-বাসরে গিয়ে দেখেছিলুম, অনেকে সত্যিই কাঁদছেন। তখন অত্যন্ত ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলুম—কড়া কথা বলা আমার অভ্যাস আছে, এ-রকম ক্ষেত্রে কড়া কথা মাঝে মাঝে বলেও থাকি—সেদিন বলেছিলুম, এখন আপনারা কেঁদে ভাসাচ্ছেন। কিন্তু জানেন কি যে, বারো বছরে তাঁর পাঁচ-শ’ খানা বই বিক্রি হয়নি? অনেকে বোধকরি তাঁর সব পুস্তকের নাম পর্যন্ত জানেন না। অথচ, আজ এসেছেন অশ্রুপাত করতে।
আমাদের বড়লোকেরা যদি অন্ততঃ সামাজিক কর্তব্য হিসাবেও বই কেনেন, অর্থাৎ যাতে দেশের লেখকদের সাহায্য হয়—এমন চেষ্টা করেন, তাতে সাহিত্যের উন্নতিই হবে। লেখকেরা উৎসাহ পাবেন, পেটে খেতে পাবেন, নিজেরা নানা বই পড়বার অবসর পাবেন। এর ফলে তাঁদের জ্ঞানবৃদ্ধি হবে, তবে ত তাঁরা ‘জ্ঞানগর্ভ’ বই লিখতে পারবেন।
রায় মহাশয়ের বক্তৃতা শুনে আর একটা কথা বেশী করে আমাদের নজরে পড়ে যে, ও-দেশের যা কিছু হয়েছে, তা করেচে ও-দেশের জনসাধারণ।
তারা মস্ত লোক। তাদেরই মোটা মোটা দানে বড় বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। আমরা প্রায়ই সরকারকে গালাগালি দিই। কিন্তু এই আমাদের দেশবন্ধুর স্মৃতিভাণ্ডার ভরল কতটুকু! তিনি দেশের জন্যে কত করেছেন। তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্যে কত আবেদনই না বেরুল। কিন্তু সে ভিক্ষাপাত্র আজও আশানুরূপ পূর্ণ হল না; অথচ ইংলণ্ডে ‘ওয়েস্টমিনস্টার এবি’র এক কোণে যখন ফাটল ধরে, সেখানকার ডীন কুড়ি লক্ষ পাউন্ডের জন্যে এক আবেদন করেন। কয়েক মাসের মধ্যে এত টাকা এল যে, শেষে তিনি সেই ফন্ড বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। অথচ দাতারা নাম বাজাবার জন্যে যে দান করেন নি তা স্পষ্ট বোঝা যায়, কারণ কাগজে কারোরই নাম বেরোয় নি। এতটা সম্ভব হয় তখনই যখন লোকের মধ্যে স্বদেশ সম্বন্ধে একটা প্রবুদ্ধ মন গড়ে ওঠে।
আমার প্রার্থনা, কুমার মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয় দীর্ঘজীবী হোন। তাঁর এই প্রারব্ধ কাজে উত্তরোত্তর সাফল্যলাভ করুন। ওঁর কথা শুনে আমাদের মনে জাগে আকুলতা। যাঁর যে পরিমাণ শক্তি লাইব্রেরি আন্দোলনের জন্যে তাই দেন ত দেশের কাজ অনেক এগিয়ে যাবে। আমাদের নিজেদের দেখার হয়ত অবসর ঘটবে না। কিন্তু আশা হয়, আজকের দিনে যাঁরা তরুণ,—যাঁরা বয়সে ছোট, তাঁরা নিশ্চয়ই এ কাজের কিছু ফল দেখতে পাবেন।
‘কোন্নগর পাঠচক্র’র চেষ্টায় এই যে সব মূল্যবান কথা শুনা গেল, তার জন্যে বক্তা এবং সভ্যদের আন্তরিক ধন্যবাদ দিই। আজ বড় আনন্দ পেলাম,—শিক্ষা পেলাম, মনের মধ্যে ব্যথাও পেলাম। কোথায় ইউরোপ আর কোথায় আমাদের দুর্ভাগা দেশ! যুগযুগান্তের পাপ সঞ্চিত হয়ে আছে। একমাত্র ভগবানের বিশেষ করুণা ছাড়া পরিত্রাণের আর ত কোন আশা দেখি না।
বাল্য-স্মৃতি
পুরাতন কথার আলোচনা-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে আমার সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা আছে, কিন্তু আছে বলিয়াই যে সে আলোচনায় আমিও যোগ দিই এ আমার স্বভাব নয়। তাহার প্রধান কারণ, আমি অত্যন্ত অলস লোক—সহজে লেখালিখির মধ্যে ঘেঁষি না; দ্বিতীয় কারণ, আমার বিগত জীবনের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে আমি অত্যন্ত উদাসীন। জানি, এ লইয়া বহুবিধ জল্পনা-কল্পনা ও নানাবিধ জনশ্রুতি সাধারণ্যে প্রচারিত আছে কিন্তু আমার নির্বিকার আলস্যকে তাহা বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতেও পারে না। শুভার্থীরা মাঝে মাঝে উত্তেজিত হইয়া আসিয়া বলেন, এইসব মিথ্যের আপনি প্রতিকার করবেন না? আমি বলি, মিথ্যে যদি থাকে ত সে প্রচার আমি করিনি, সুতরাং প্রতিকার করার দায় আমার নয়—তাঁদের। তাঁদের করতে বলো গে। তাঁরা রাগিয়া জবাব দেন—লোকে যে আপনাকে অদ্ভুত ভাবে তার কি? আমি বলি, সে-দায়ও তাঁদের, কিন্তু এই সাতান্ন বছরেও যদি ক্ষতি না হয়ে থাকে ত আর কয়েকটা বছর ধৈর্য ধরে থাকো—আপনিই এর সমাপ্তি হবে। কোন চিন্তা নেই।
আজ…এই লেখাটা পড়িতে পড়িতে ভাবিতেছিলাম আমাদের ছেলেবেলার সেই অতি ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর সাহিত্য-সভায়…নেপথ্যে যোগদান করার—‘নেপথ্য’ শব্দটি কে একজন দিতে ভুলিয়াছেন বলিয়া…কি অস্থিরতা! একবারও ভাবিয়া দেখি নাই কতটুকুই ইহার মূল্য এবং জগৎ-সংসারে কেই-বা সে-কথা মনে রাখিবে। অবশ্যই ইহার জবাবও আছে।
সে যাই হোক, নিজের কথাটাই বলি। বলার একটু হেতু আছে,—কিন্তু সে আমার নিজের জন্য নয়—এ লেখার শেষ পর্যন্ত পড়িলে তাহা বুঝা যাইবে।
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আমার আত্মীয় ও আবাল্যবন্ধু। ‘কল্লোলে’ এবং ‘কালি-কলমে’ তিনি আমার বাল্যজীবনের প্রসঙ্গে কি-কি লিখিয়াছেন আমি পড়ি নাই—কোন্ কথা বলিয়াছিলেন তাহাও দেখি নাই। এ-ও আমার স্বভাব। কিন্তু আমি জানি, আমার প্রতি সুরেনের কি অপরিসীম স্নেহ, সুতরাং তাঁহার লেখায় অতিশয়োক্তি যে আছেই তাহা না পড়িয়াও হলফ করিতে পারি। কিন্তু না পড়িয়া হলফ করা এক কথা,—এবং না পড়িয়া প্রতিবাদ করা অন্য কথা। অতএব ইহা কাহারও লেখার প্রতিবাদ নয়,—শুধু যতটুকু আমার মনে পড়ে তাহাই বলা।
ভাগলপুরে আমাদের সাহিত্য-সভা যখন স্থাপিত হয় তখন আমাদের সঙ্গে শ্রীমান বিভূতিভূষণ ভট্ট বা তাঁর দাদাদের কিছুমাত্র পরিচয় ছিল না। বোধ হয় একটা কারণ এই যে, তাঁরা ছিলেন বিদেশী এবং বড়লোক।…স্বর্গীয় নফর ভট্ট ছিলেন সেখানকার সবজজ। তারপরে কি করিয়া এই পরিবারের সঙ্গে আমাদের ক্রমশঃ জানাশুনা এবং ঘনিষ্ঠতা হয় সে-সব কথা আমার ভালো মনে নাই। বোধ হয় এই জন্য যে, ধনী হইলেও ইঁহাদের ধনের উগ্রতা বা দাম্ভিকতা কিছুমাত্র ছিল না। এবং আমি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম বোধ হয় এইজন্য বেশী যে, ইঁহাদের গৃহে দাবা-খেলার অতি পরিপাটি আয়োজন ছিল। দাবা-খেলার পরিপাটি আয়োজন অর্থে বুঝিতে হইবে—খেলোয়াড়, চা, পান ও মুহুর্মুহুঃ তামাক।
সম্ভবতঃ এই সময়েই…শ্রীমান বিভূতিভূষণ আমাদের সাহিত্য-সভায় সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন। আমি ছিলাম সভাপতি, কিন্তু আমাদের সাহিত্য-সভায়…গুরুগিরি করিবার অবসর অথবা প্রয়োজন আমার কোনকালেই ঘটে নাই। সপ্তাহে একদিন করিয়া সভা বসিত এবং অভিভাবক গুরুজনদের চোখ এড়াইয়া কোন একটি নির্জন মাঠেই বসিত। জানা আবশ্যক যে, সে-সময়ে সে-দেশে সাহিত্যচর্চা একটা গুরুতর অপরাধের মধ্যেই গণ্য ছিল। এই সভায় মাঝে মাঝে…কবিতা পাঠ করা হইত। গিরীন পড়িতে পারিত সবচেয়ে ভালো, সুতরাং এ-ভার তাহার উপরেই ছিল, আমার ’পরে নয়। কবিতার দোষগুণ বিচার হইত এবং উপযুক্ত বিবেচিত হইলে সাহিত্য-সভার মাসিকপত্র ‘ছায়া’য় প্রকাশিত হইত। গিরীন ছিলেন একাধারে সাহিত্য-সভার সম্পাদক, ‘ছায়া’র সম্পাদক ও ‘অঙ্গুলি-যন্ত্রে’ অধিকাংশ লেখার মুদ্রাকর। এ-সম্বন্ধে এই আমার মোটামুটি মনে পড়ে।
সাহিত্য-সভার সভ্যগণের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী ছিলেন…বিভূতি। যেমন ছিল তাঁর পড়াশুনা বেশী, তেমনি ছিলেন তিনি ভদ্র এবং বন্ধুবৎসল। সমঝদার-সমালোচকও তেমনি।…
কিন্তু না বলিয়া জানা এবং না-বলিয়া প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করাও ঠিক এক বস্তু নয়। তখন সঙ্কোচে বাধা দেয়, বয়োজ্যেষ্ঠ কাহাকেও অকারণে ক্ষুণ্ণ করার ক্ষোভে মন অশান্তি বোধ করে। অথচ সত্য-প্রতিষ্ঠা যখন করিতেই হয় তখন অপ্রিয় কর্তব্যের এই পুনঃপুনঃ দ্বিধা নিজের বক্তব্যকে পদে পদে অস্বচ্ছ করিয়া তোলে।
পুরাতন কথার আলোচনায়…বিপদ হইয়াছে এইখানে। অথচ প্রয়োজন ছিল না। এই সুদীর্ঘ বর্ষ পরে আমি হইলে বলিতাম, কত ভুলই ত সংসারে আছে, থাকিলই বা আর একটা। কি এমন ক্ষতি! কিন্তু আমার ও অপরের ক্ষতিবোধের হিসাব ত এক নয়।
…এখানে একটা গল্প মনে পড়িয়াছে। গল্পটা এই—
“কয়েক বৎসরের কথা, একবার হাবড়ায় ‘শরৎচন্দ্র’ সম্বন্ধীয় একটি সভার একজন বক্তা বোধ হয় সুরেন্দ্রনাথের ঐ লেখাটি পড়িয়াই (‘কল্লোল’ মাঘ, ১৩৩২) বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, টিলাকুঠির মাঠে (ভাগলপুর) এই সভা বসিত এবং সুরেন্দ্র, গিরীন্দ্র…বিভূতিভূষণ তাঁহার পদতলে বসিয়া সাহিত্য-সাধনা করিত। এই সভার একজন শ্রোতা (তাঁর নাম ৺বিনয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শারীরিক বলের জন্য আদমপুর ক্লাবে এই বিনয়বাবুকে সকলেই জানিত। তিনি গৃহশিক্ষকরূপে ভাগলপুরে বহুদিন বাস করায়…সবই জানিতেন।) উত্তেজিত হইয়া আমাদের এ-খবর দেন এবং প্রতিবাদ করিতে বলেন। বিভূতিবাবু তাঁহাকে বহু কষ্টে প্রকৃতিস্থ করিয়া বুঝান যে…অপরের মুখের শোনা-কথা লেখায় প্রতিবাদ চলে না। আপনি মুখে যাহা বলিয়াছেন সেই পর্যন্তই ভাল।”
বিভূতিবাবু তাঁহার ভূতপূর্ব গৃহশিক্ষক বিনয়কুমারকে যদি সত্যই ‘প্রকৃতিস্থ’ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন ত একটা বিস্ময়কর ব্যাপার করিয়াছিলেন তাহা মানিবই। কারণ, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এক ঘণ্টাও তাঁহাকেও ‘প্রকৃতিস্থ’ করা সহজ বস্তু ছিল না। “পদতলে বসিয়া সাহিত্য-সাধনা করিত”, সভায় এই গ্লানিকর উক্তি শুনিয়া ভূতপূর্ব গৃহশিক্ষক বিনয়কুমার নিজে উত্তেজিত হইয়া প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং অপরকে উত্তেজিত হইতে প্ররোচিত করিয়াছেন। কিন্তু ঘটনাটা আমার কাছে একেবারে নূতন। ১৩৩২ সনে আমি হাবড়াতেই ছিলাম অথচ আমার সম্বন্ধে এরূপ একটা সভা হওয়ার কথা আমি আদৌ বিদিত নই। সভা সত্যিই হইয়া থাকিলে এবং নিজে উপস্থিত থাকিলে এমন একটা কথা আমার নিজের পক্ষে যত বড় গৌরবের সামগ্রীই হোক অসত্য বলিয়া নিশ্চয়ই প্রতিবাদ করিতাম এবং বিনয়েরও উত্তেজিত হইয়া উঠার প্রয়োজন হইত না। তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।
…মানুষ স্বভাবতঃ অনেকটা যে কল্পনাপ্রবণ তাহা সত্য এবং কল্পনারও যে উপযোগিতা আছে তাহাও সত্য, কিন্তু যথাস্থানে। ভূতপূর্ব গৃহশিক্ষক বিনয়কুমার পরবর্তীকালে ছিলেন Statesman কাগজের Reporter. বার বার ঘটনাস্থলে উপস্থিত না থাকিয়াও খরতর কল্পনার সাহায্যে report দাখিল করার জন্য তাঁহার চাকরি গিয়াছিল এবং কাগজের সম্পাদককেও লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল।
আজ বিনয় পরলোকগত। মৃত ব্যক্তিকে লইয়া এই সকল কথা লিখিতে আমার ক্লেশবোধ হয়।…
কিন্তু ইহা বাহ্য। আসলে…উত্ত্যক্ত করিয়াছে কতকগুলি অতি কৌতূহলী লোকের অশিষ্ট…ও অমার্জনীয় জিজ্ঞাসাবাদ। তাহারা প্রশ্ন করিয়াছে, আমার কাছে…সাহিত্য-ব্যাপারে কে কতটা ঋণী। লোকেরা এ-প্রশ্ন আমাকেও যে না করিয়াছে তাহা নয়। কিন্তু যে-কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছে তাহাকেই অকপটে এই সত্য কথাটাই চিরদিন বলিয়াছি যে…আমার কাছে লেশমাত্র কেহ ঋণী নয়। একস্থানে এক সময়ে ছেলে-বয়েসে সাহিত্যচর্চা করিতে থাকিলে লোক পরস্পরকে উৎসাহ দিয়াই থাকে, ভালো লাগিলে ভালো বলিয়া বন্ধুজনেরা অভিনন্দিত করিয়াই থাকে, তাহাকে ঋণ বলিয়া অভিহিত করিতে গেলে মানুষের ঋণের কোথাও আর সীমা থাকে না। যেমন সুরেন, গিরীন, উপেন, তেমনি বিভূতি…প্রভৃতি। লেখা পড়িয়া ভালো লাগিলে ভালো বলিয়াছি—কোথাও তেমন ভালো না লাগিলে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া আবার লিখিতে অনুরোধ করিয়াছি।…কোনদিন সংশোধন করি নাই।…এতকাল পরে এই সকল কথা ব্যক্ত করার উদ্দেশ্য আমার শুধু এই যে, এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য যেন লিপিবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে।…
এইবার আমার নিজের সম্বন্ধে দুই-একটা কথা বলিয়া এ-আলোচনা শেষ করিতে চাই। ছেলেবেলার লেখা কয়েকটা বই আমার নানা কারণে হারাইয়া গেছে। সবগুলার নাম আমার মনে নাই। শুধু…দু’খানা বইয়ের নষ্ট হওয়ার বিবরণ জানি। একখানা, ‘অভিমান’, মস্ত মোটা খাতায় স্পষ্ট করিয়া লেখা,—অনেক বন্ধুবান্ধবের হাতে হাতে ফিরিয়া অবশেষে গিয়া পড়িল বাল্যকালের সহপাঠী কেদার সিংহের হাতে। কেদার অনেকদিন ধরিয়া অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু ফিরিয়া পাওয়া আর গেল না। এখন তিনি এক ঘোরতর তান্ত্রিক সাধুবাবা। বইখানা কি করলেন তিনিই জানেন—কিন্তু চাহিতে ভরসা হয় না—তাঁর সিঁদুর মাখানো মস্ত ত্রিশূলটার ভয় করি। এখন তিনি নাগালের বাহিরে—মহাপুরুষ—ঘোরতর তান্ত্রিক সাধুবাবা।
দ্বিতীয় বই ‘শুভদা’। প্রথম যুগের লেখা ওটা ছিল আমার শেষ বই, অর্থাৎ ‘বড়দিদি’, ‘চন্দ্রনাথ’, ‘দেবদাস’ প্রভৃতির পরে।
বেতার-সঙ্গীত
শহর হইতে দূরে গ্রামের মধ্যে আমার বাস। অতীতের নানাপ্রকার আমোদ ও আনন্দের প্রাত্যহিক আয়োজন গ্রামে আর নাই, পল্লী এখন নির্জীব নিরানন্দ। কর্মক্লান্ত দিনের কত সন্ধ্যায় এই নিঃসঙ্গ পল্লীভবনে বেতারের জন্য উৎসুক আগ্রহে অপেক্ষা করিয়াছি। শ্রাবণের ঘন মেঘে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া আসে, কর্দমাক্ত জনহীন গ্রাম্যপথ নিতান্ত দুর্গম, নিবিড় অন্ধকার ভারের মত বুকের ’পরে চাপিয়া বসে, তখন বেতার-বাহিত গানের পালায় মনে হয় যেন দূরে থাকিয়াও আসরের ভাগ পাইতেছি।
আবার কোন দিন ক্ষান্তবর্ষণ আকাশে লঘু মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো দেখা দেয়, বর্ষার সুবিস্তীর্ণ নদী-জলে মলিন জ্যোৎস্না ছড়াইয়া পড়ে, আমি তখন প্রাঙ্গণের একান্তে নদীতটে আরাম-কেদারায় চোখ বুজিয়া বসি, তামাকের ধুঁয়ার সঙ্গে মিশিয়া বেতার বাঁশীর সুর যেন মায়াজাল রচনা করে। দু-একজন করিয়া প্রতিবেশী জুটিতে থাকে, ঘাটে বাঁধা নৌকায় দূরের যাত্রী, কৌতূহলী, দাঁড়ি-মাঝির দল নিঃশব্দে আসিয়া ঘিরিয়া বসে, আবার শেষ হইলে পরিতৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া যে যাহার আলয়ে চলিয়া যায়। এই আনন্দের অংশ আমি পাই।
ভাগ্য-বিড়ম্বিত লেখক-সম্প্রদায়
সেদিন গুণে দেখলাম—সত্যিকার সাধনা যাঁরা করেন, সাহিত্য যাঁদের শুধু বিলাস নয়, সাহিত্য যাঁদের জীবনের একমাত্র ব্রত, বাঙলাদেশে তাঁরা ক’জনই বা, সংখ্যা আঙুলে গোণা যায়।
এই-সব সাহিত্যসেবী অক্লান্ত পরিশ্রম করে অনাহারে অনিদ্রায় দেশের জন্য দশের জন্য সাহিত্য সৃষ্টি করেন, সে সাহিত্য শুনেছি নাকি জন-সমাজের কল্যাণ করে, কিন্তু তার কি মূল্য আমরা দিয়ে থাকি?
এই যে সব সাহিত্যিক দেশের জন্য প্রাণপণ করেছেন, তাঁদের পুরস্কার হয়েছে শুধু লাঞ্ছনা আর দারিদ্র। প্রভূত ধন-সম্পত্তি অর্জন করে, বিত্তশালী ধনবান হতে তাঁরা চান না, তাঁরা চান শুধু একটুখানি স্বচ্ছন্দ জীবন, সর্বনাশা দারিদ্র্যের নিদারুণ অভিশাপ থেকে মুক্তি, তাঁরা চান শুধু নিশ্চিত নির্ভাবনায় লিখবার মত একটুখানি অনুকূল আবহাওয়া, অথচ তাঁরা তাও পান না। আজীবন শুধু ভাগ্য-বিড়ম্বিত হয়েই তাঁদের কাটাতে হয়, যাদের কল্যাণ কামনায় তাঁরা জীবন উৎসর্গ করলেন তারা একবার সেদিকে ফিরেও তাকায় না।
দেশের লোক তাঁদের দেয় না কিছু, অথচ, তাঁদের কাছ থেকে চায় অনেক। কোথাও কেউ যদি এতটুকু খারাপ লেখা লিখেছে, অমনি তীব্র সমালোচনার বিষে আর নিন্দার তীক্ষ্ণ শরে তাঁকে জর্জরিত হতে হয়।
এই অতিনিন্দিত গল্প-লেখকদের দৈন্যের সীমা নেই। এঁদের লেখা পড়ে জনসাধারণ আনন্দ লাভ করে সত্য, কিন্তু তাঁদের ঘরের খবর নিতে গেলে দেখতে পাবেন—এই-সব লেখক-সম্প্রদায় কত নিঃস্ব, কত অসহায়। অনেকেরই উপন্যাসের হয়ত দ্বিতীয় সংস্করণ হয় না।
কিন্তু কেন?
এর একমাত্র কারণ, আমাদের দেশের লোক বই পড়েন বটে, কিন্তু পয়সা খরচ করে কিনে পড়েন না। এমন কথা হয়ত উঠতে পারে যে, আমাদের দেশের জনসাধারণ দরিদ্র, বই কেনবার সামর্থ্য তাঁদের নেই। কিন্তু সামর্থ্য যাঁদের আছে, এমন অনেক বড়লোকের বাড়িতে আমি নিজে গেছি, গিয়ে দেখেচি, তাঁদের আছে সবই, গাড়ি আছে, বাড়ি আছে, বিলাস-ব্যসনের সহস্র উপকরণ আছে, নেই কেবল বই। পয়সা খরচ করে বই কেনা তাঁদের অনেকের কাছেই অপব্যয় ছাড়া আর কিছু নয়।
অথচ গল্প-লেখকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের আর অন্ত নেই। সম্প্রতি একটা কথা শুনছি, ভাল লেখা তাঁরা লিখছেন না। কেন লিখছেন না আমাকে যদি কেউ প্রশ্ন করেন ত আমি বলব—শক্তি যাঁদের আছে অর্থের অভাবে দারিদ্র্যের তাড়নায় আজ তাঁরা এমনি নিষ্পেষিত যে, ভাল কিছু লিখবার ইচ্ছা থাকলেও অবসর বা স্পৃহা তাঁদের নেই।
এর প্রতিকার সর্বাগ্রে প্রয়োজন। সর্বাগ্রে আমাদের দেশের সাহিত্যিকদের অভাব-মোচনের ব্যবস্থা করতে হবে, ভাল লেখা যাতে তাঁরা লিখতে পারেন তার অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে হবে। তবেই বাংলা সাহিত্য বাঁচবে, নইলে অচির-ভবিষ্যতে কি যে তার অবস্থা হবে, ভগবানই জানেন।
আমাদের দেশের বড়লোকেরা অন্ততঃ কর্তব্যের খাতিরেও যদি একখানা করে বই কেনেন তা হলেও বা এর প্রতিকারের কিছু ব্যবস্থা হয়। বই না কিনেও অনেক রকমে তাঁরা সাহায্য করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলতে পারেন। কিন্তু তা তাঁরা করবেন কি?
আগেকার দিনে বড় বড় রাজারাজড়ারা সভাকবি রেখে কবি, সাহিত্যিকের বৃত্তির ব্যবস্থা করে অনেক রকমে দেশের সাহিত্যকে বড় হবার সুযোগ দিতেন। আজকাল তাও নেই।
শখের সাহিত্যিকদের কথা আমি বলচি না। ভগবানের কৃপায় অন্নের সংস্থান যাঁদের আছে, সাহিত্য যাঁদের বিলাসের সামগ্রী, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা হয়ত বলবেন—অন্নচিন্তাটা ভাল্গার, সুতরাং সাহিত্যের শ্রী ওতে নষ্ট হবে, সে চিন্তা পরে করলেও চলবে।
পরে চিন্তা করলেও যাঁদের চলে তাঁরা তাই করুন, তাঁদের কথা এখানে তুলব না। আমি শুধু সেই-সব দুর্ভাগাদের কথাই বলছি—যাদের অস্থিতে মজ্জায় সাহিত্যের অত্যুগ্র বিষের ক্রিয়া শুরু হয়েছে, সাহিত্যসৃষ্টি যাদের জন্ম-অধিকার, যাদের রক্তের মধ্যে সৃষ্টির উন্মাদনা।
এই-সব উন্মাদেরা সহস্র দারিদ্র্য-লাঞ্ছনার মধ্যে বসেও লিখবে আমি জানি। না লিখলে তারা বাঁচবে না। তাই যতদিন তারা বেঁচে থাকে তাদের মুখে দু-মুঠো অন্ন তুলে দিতে চাই। এই-সব পরার্থে উৎসর্গীকৃত জীবনের শিখা অন্নাভাবে অকালে যদি নির্বাপিত হয়ে যায়—দেশের কল্যাণ তাতে হবে না, এইটুকু আজ আপনারা জেনে রাখুন। * (‘বাতায়ণ’ ২৭ ফাল্গুন, ১৩৪৪, শরৎ-স্মৃতিসংখ্যা)
মহাত্মাজী
মহাত্মাজী আজ রাজার বন্দী। ভারতবাসীর পক্ষে এ সংবাদ যে কি, সে কেবল ভারতবাসীই জানে। তবুও সমস্ত দেশ স্তব্ধ হইয়া রহিল। দেশব্যাপী কঠোর হরতাল হইল না, শোকোন্মত্ত নরনারী পথে পথে বাহির হইয়া পড়িল না, লক্ষ কোটি সভা-সমিতিতে হৃদয়ের গভীর ব্যথা নিবেদন করিতে কেহ আসিল না—যেন কোথাও কোন দুর্ঘটনা ঘটে নাই,—যেমন কাল ছিল, আজও সমস্তই ঠিক তেমনি আছে, কোনখানে একটি তিল পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয় নাই—এমনিভাবে আসমুদ্র-হিমাচল নীরব হইয়া আছে। কিন্তু এমন কেন ঘটিল? এতবড় অসম্ভব কাণ্ড কি করিয়া সম্ভবপর হইল? নীচাশয় অ্যাংলো- ইণ্ডিয়ান কাগজগুলা যাহার যাহা মুখে আসিতেছে বলিতেছে, কিন্তু প্রতিদিনের মত সে মিথ্যা খণ্ডন করিতে কেহ উদ্যত হইল না। আজ কথা-কাটাকাটি করিবার প্রবৃত্তি পর্যন্ত কাহারও নাই। মনে হয়, যেন তাহাদের ভারাক্রান্ত হৃদয়ের গভীরতম বেদনা আজ সমস্ত তর্ক-বিতর্কের অতীত।
যাইবার পূর্বাহ্ণে মহাত্মাজী অনুরোধ করিয়া গেছেন, তাঁহার জন্য কোথাও কোন হরতাল, কোনরূপ প্রতিবাদ-সভা, কোনপ্রকার চাঞ্চল্য বা লেশমাত্র আক্ষেপ উত্থিত না হয়। অত্যন্ত কঠিন আদেশ। কিন্তু তথাপি সমস্ত দেশ তাঁহার সে আদেশ শিরোধার্য করিয়া লইয়াছে। এই কণ্ঠরোধ, এই নিঃশব্দ সংযম, আপনাকে দমন করিয়া রাখার এই কঠোর পরীক্ষা যে কত বড় দুঃসাধ্য, এ কথা তিনি ভাল করিয়াই জানিতেন, তবুও এ আজ্ঞা প্রচার করিয়া যাইতে তাঁহার বাধে নাই। আর একদিন—যেদিন তিনি বিপন্ন দরিদ্র উপদ্রুত ও বঞ্চিত প্রজার পরম দুঃখ রাজার গোচর করিতে যুবরাজের অভ্যর্থনা নিষেধ করিয়াছিলেন, এই অর্থহীন নিরানন্দ উৎসবের অভিনয় হইতে সর্বতোভাবে বিরত হইতে প্রত্যেক ভারতবাসীকে উপদেশ দিয়াছিলেন, সে দিনেও তাঁহার বাধে নাই। রাজরোষাগ্নি যে কোথায় এবং কত দূরে উৎক্ষিপ্ত হইবে, ইহা তাঁহার অবিদিত ছিল না, কিন্তু কোন আশঙ্কা, কোন প্রলোভনই তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। ইহাকে উপলক্ষ করিয়া দেশের উপর দিয়া কত ঝঞ্ঝা কত বজ্রপাত কত দুঃখই না বহিয়া গেল, কিন্তু, একবার সত্য ও কর্তব্য বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, যুবরাজের উৎসব-সম্বন্ধে শেষ দিন পর্যন্ত সে আদেশ তাঁহার প্রত্যাহার করেন নাই। তার পর অকস্মাৎ একদিন চৌরিচৌরার ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিল। নিরুপদ্রব সম্বন্ধে দেশবাসীর প্রতি তাঁহার বিশ্বাস টলিল,—তখন এ কথা সমস্ত জগতের কাছে অকপট ও মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিতে তাঁহার লেশমাত্র দ্বিধাবোধ হইল না।
নিজের ভুল ও ত্রুটি বারংবার স্বীকার করিয়া বিরুদ্ধ রাজশক্তির সহিত আসন্ন ও সুতীব্র সংঘর্ষের সর্বপ্রকার সম্ভাবনা স্বহস্তে রোধ করিয়া দিলেন। বিন্দুমাত্রও কোথাও তাঁহার বাধিল না। সিন্ধু হইতে আসাম ও হিমাচল হইতে দাক্ষিণাত্যের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত অসহযোগপন্থীদের মুখ হতাশ্বাস ও নিষ্ফল ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল এবং অনতিকালবিলম্বে দিল্লীর নিখিল-ভারতীয় কংগ্রেস কার্যকরী সভায় তাঁহার মাথার উপর দিয়া গুপ্ত ও ব্যক্ত লাঞ্ছনার যেন একটা একটা ঝড় বহিয়া গেল। কিন্তু তাঁহাকে টলাইতে পারিল না। একদিন যে তিনি সবিনয়ে ও অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিয়াছিলেন I have lost all fear of men—জগদীশ্বর ব্যতীত মানুষকে আমি ভয় করি না—এ সত্য কেবল প্রতিকূল রাজশক্তির কাছে নয়, একান্ত অনুকূল সহযোগী ও ভক্ত অনুচরদিগের কাছেও সপ্রমাণ করিয়া দিলেন। রাজপুরুষ ও রাজশক্তির অনাচার ও অত্যাচারের তীব্র আলোচনা এ দেশে নির্ভয়ে আরও অনেকে করিয়া গেছেন, তাহার দণ্ডভোগও তাঁহাদের ভাগ্যে লঘু হয় নাই, তথাপি ভয়হীনতার পরীক্ষা তাঁহাদিগকে কেবল এই দিক দিয়াই দিতে হইয়াছে। কিন্তু ইহাপেক্ষাও যে বড় পরীক্ষা ছিল,—অনুরক্ত ও ভক্তের অশ্রদ্ধা, অভক্তি ও বিদ্রূপের দণ্ড—এ কথা লোকে একপ্রকার ভুলিয়াছিল—যাবার পূর্বে দেশের কাছে এই পরীক্ষাটাই তাঁহাকে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে হইল। অত্যন্ত স্পষ্ট করিয়া দেখিয়া যাইতে হইল যে—সম্ভ্রম, মর্যাদা, যশঃ, এমন কি কি জন্মভূমির উপরেও সত্যকে প্রতিষ্ঠা করিতে না পারিলে ইহা পারা যায় না। কিন্তু এত বড় শান্ত শক্তি ও সুদৃঢ় সত্যনিষ্ঠার মর্যাদা ধর্মহীন উদ্ধত রাজশক্তি উপলব্ধি করিতে পারিল না, তাঁহাকে লাঞ্ছনা করিল। মহাত্মাকে সেদিন রাত্রে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। কিছু কাল হইতে এই সম্ভাবনা জনশ্রুতিতে ভাসিতেছিল, অতএব ইহা আকস্মিকও নয়, আশ্চর্যও নয়। কারাদণ্ড অনিবার্য। ইহাতেও বিস্ময়ের কিছু নাই। কিন্তু ভাবিবার কথা আছে। ভাবনা ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার নিজের জন্য নয়, এ চিন্তা সমষ্টিগত ভাবে সমস্ত দেশের জন্য। যিনি একান্ত সত্যনিষ্ঠ, যিনি কায়মনোবাক্যে অহিংস, স্বার্থ বলিয়া যাঁহার কোথাও কোন কিছু নাই, আর্তের জন্য পীড়িতের জন্য সন্ন্যাসী,—এ দুর্ভাগা দেশে এমন আইনও আছে, যাহার অপরাধে এই মানুষটিকেও আজ জেলে যাইতে হইল।
দেশের মঙ্গলেই রাজশ্রীর মঙ্গল, প্রজার কল্যাণেই রাজার কল্যাণ, শাসনতন্ত্রের এই মূল তত্ত্বটি আজ এ দেশে সত্য কি না, এখানে দেশের হিতার্থেই রাজ্য পরিচালনা, প্রজার ভাল হইলেই রাজার ভাল হয় কি না, ইহা চোখ মেলিয়া আজ দেখিতে হইবে।আত্ম-বঞ্চনা করিয়া নয়, পরের উপর মোহ বিস্তার করিয়া নয়, হিংসা ও আক্রোশের নিষ্ফল অগ্নিকাণ্ড করিয়া নয়,—কারারুদ্ধ মহাত্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, তাঁহারি মত শুদ্ধ ও সমাহিত হইয়া এবং তাঁহারি মত লোভ, মোহ ও ভয়কে সকল দিক দিয়া জয় করিয়া।অর্থহীন কারাবরণ করিয়া নয়,—কারাবরোধের অধিকার অর্জন করিয়া।
হয়ত ভালই হইয়াছে। শাসনযন্ত্রের নাগপাশে আজ তিনি আবদ্ধ। তাঁহার একান্ত বাঞ্ছিত বিশ্রামের কথাটা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, কিন্তু দেশের ভার যখন আজ দেশের মাথায় পড়িল,—একটা কথা যে তিনি বারবার বলিয়া গিয়াছেন, দানের মত স্বাধীনতা কোনদিন কাহারও হাত হইতে গ্রহণ করা যায় না, গেলেও তাহা থাকে না, ইহাকে হৃদয়ের রক্ত দিয়া অর্জন করিতে হয়—তাঁহার অবর্তমানে আপনাকে সার্থক করিবার এই পরম সুযোগটাই হয়ত আজ সর্বসাধারণের ভাগ্যে জুটিয়াছে। যাহারা রহিল, তাহারা নিতান্তই মানুষ। কিন্তু মনে হয়, অসামান্যতার পরম গৌরব আজ কেবল তাহাদেরই প্রতীক্ষা করিয়া রহিল।
আরও একটা পরম সত্য তিনি অত্যন্ত পরিস্ফুট করিয়া গেছেন। কোন দেশ যখন স্বাধীন, সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তখন দেশাত্মবোধের সমস্যাও খুব জটিল হয় না, স্বদেশ-প্রেমের পরীক্ষাও একেবারে নিরতিশয় কঠোর করিয়া দিতে হয় না। সে দেশের নেতৃস্থানীয়গণকে তখন পরম যত্নে বাছাই করিয়া না লইলেও হয়ত চলে। কিন্তু সেই দেশ যদি কখনও পীড়িত, রুগ্ন ও মরণাপন্ন হইয়া উঠে, তখন ঐ ঢিলাঢালা কর্তব্যের আর অবকাশ থাকে না। তখন এই দুর্দিন যাঁহারা পার করিয়া লইয়া যাইবার ভার গ্রহণ করেন, সকল দেশের সমস্ত চক্ষের সম্মুখে তাঁহাদিগকে পরার্থপরতার অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়। বাক্যে নয়—কাজে, চালাকির মারপ্যাঁচে নয়—সরল সোজা পথে, স্বার্থের বোঝা বহিয়া নয়—সকল চিন্তা, সকল উদ্বেগ, সকল স্বার্থ জন্মভূমির পদপ্রান্তে নিঃশেষে বলি দিয়া। ইহার অন্যথা বিশ্বাস করা চলে না। এই পরম সত্যটিকে আর আমাদের বিস্মৃত হইলে কোনমতে চলিবে না। এই পরীক্ষা দিতে গিয়াই আজ শত-সহস্র ভারতবাসী রাজকারাগারে। এবং এইজন্যই ইহাকে ‘স্বরাজ আশ্রম’ নাম দিয়াও তাঁহারা আনন্দে রাজদণ্ড মাথায় পাতিয়া লইয়াছেন।
প্রজার কল্যাণের সহিত রাজশক্তির আজ কঠিন বিরোধ বাধিয়াছে।
এই বিগ্রহ, এই বোঝাপড়া কবে শেষ হইবে, সে শুধু জগদীশ্বরই জানেন, কিন্তু রাজায়-প্রজায় এই সংঘর্ষ প্রজ্বলিত করিবার যিনি সর্বপ্রধান পুরোহিত, আজ যদিও তিনি অবরুদ্ধ, কিন্তু এই বিরোধের মূল তথ্যটা আবার একবার নূতন করিয়া দেখিবার সময় আসিয়াছে। সংশয় ও অবিশ্বাসই সকল সদ্ভাব, সকল বন্ধন, সকল কল্যাণ পলে পলে ক্ষয় করিয়া আসিতেছে। শাসনতন্ত্র কহিলেন, “এই”, প্রজাপুঞ্জ জবাব দিতেছে,—“না, এই নয়, তোমার মিথ্যা কথা।” রাজশক্তি কহিতেছেন, “তোমাকে এই দিব, এতদিনে দিব।” প্রজাশক্তি চোখ তুলিয়া, মাথা নাড়িয়া বলিতেছে, “তুমি আমাকে কোনদিন কিছু দিবে না,—নিছক বঞ্চনা করিতেছ।”
“কে বলিল?”
“কে বলিল! আমার সমস্ত অস্থিমজ্জা, আমার সমস্ত প্রাণশক্তি, আমার আত্মা, আমার ধর্ম, আমার মনুষ্যত্ব, আমার পেটের সমস্ত নাড়িভুঁড়িগুলা পর্যন্ত তারস্বরে চীৎকার করিয়া কেবল এই কথা ক্রমাগত বলিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু শোনে কে? চিরদিন তুমি শুনিবার ভান করিয়াছ, কিন্তু শোন নাই। আজও সেই পুরানো অভিনয় আর একবার নূতন করিয়া করিতেছ মাত্র। তোমাকে শুনাইবার ব্যর্থ চেষ্টায় জগতের কাছে আমার লজ্জা ও হীনতার অবধি নাই; কিন্তু আর তাহাতে প্রবৃত্তি নাই। তোমার কাছে নালিশ করিব না, শুধু আর একবার আমার বেদনার কাহিনীটা দেশের কাছে একে একে ব্যক্ত করিব।”
ভূতপূর্ব ভারত-সচিব মন্টেগু সাহেব সেবার যখন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, তখন এই বাঙ্গালাদেশেরই একজন বিশ্ববিখ্যাত বাঙ্গালী তাঁহাকে একখানা বড় পত্র লিখিয়াছিলেন, এবং তাহার মস্ত একটা জবাবও পাইয়াছিলেন। কিন্তু সেই আগাগোড়া ভাল ভাল ফাঁকা কথার বোঝায় ভরা চিঠিখানির ফাঁকিটুকু ছাড়া আর কিছুই আমার মনে নাই, এবং বোধ করি মনেও থাকে না। কিন্তু এ-পক্ষের মোট বক্তব্যটা আমার বেশ স্মরণ আছে। ইনি বারবার করিয়া, এবং বিশদ করিয়া ওই বিশ্বাস-অবিশ্বাসের তর্কটাই চার পাতা চিঠি ভরিয়া সাহেবকে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে, বিশ্বাস না করিলে বিশ্বাস পাওয়া যায় না। যেন এতবড় নূতন তত্ত্বকথা এই ভারতভূমি ছাড়া বিদেশী সাহেবের আর কোথাও শুনিবার সম্ভাবনা ছিল না। অথচ আমার বিশ্বাস, সাহেবের বয়স অল্প হইলেও এ তত্ত্ব তিনি সেই প্রথমও শুনেন নাই এবং সেই প্রথমও জানিয়া যান নাই। কিন্তু জানা এক এবং তাহাকে মানা আর। তাই সাহেবকে কেবল এমন সকল কথা এবং ভাষা ব্যবহার করিতে হইয়াছিল, যাহা দিয়া চিঠির পাতা ভরে, কিন্তু অর্থ হয় না।
কিন্তু কথাটা কি বাস্তবিকই সত্য? জগতে কোথাও কি ইহার ব্যতিক্রম নাই? গভর্নমেন্ট আমাদের অর্থ দিয়া বিশ্বাস করেন না, পল্টন দিয়া বিশ্বাস করেন না, পুলিশ দিয়া বিশ্বাস করেন না, ইহা অবিসম্বাদী সত্য। কিন্তু শুধু কেবল এই জন্যই কি আমরাও বিশ্বাস করিব না এবং এই যুক্তিবলেই দেশের সর্বপ্রকার রাজকার্যের সহিত অসহযোগ করিয়া বসিয়া থাকিব? গভর্নমেন্ট ইহার কি কি কৈফিয়ত দিয়া থাকেন জানি না, খুব সম্ভব কিছুই দেন না, দিলেও হয়ত ওই মন্টেগু সাহেবের মতই দেন—যাহার মধ্যে বিস্তর ভাল কথা থাকে, কিন্তু মানে থাকে না। কিন্তু তাঁহাদের অফিসিয়াল বুলি ছাড়িয়া যদি স্পষ্ট করিয়া বলেন, “তোমাদের এইসকল দিয়া বিশ্বাস করি না খুব সত্য কথা, কিন্তু সে শুধু তোমাদেরই মঙ্গলের নিমিত্ত।”
আমরা রাগ করিয়া জবাব দিই “ও আবার কি কথা? বিশ্বাস কি কখনও একতরফা হয়? তোমরা বিশ্বাস না করিলে আমরাই বা করিব কি করিয়া?”
অপর পক্ষ হইতে যদি পালটা জবাব আসিত, ও বস্তুটা দেশ-কাল-পাত্রভেদে একতরফা হওয়া অসম্ভবও নয়, অস্বাভাবিকও নয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র গলার জোরেই জয়ী হওয়া যাইত না। এবং প্রতিপক্ষ সাধারণ একটা উদাহরণের মত যদি কহিতেন, পীড়িত রুগ্ন ব্যক্তি যখন অস্ত্রচিকিৎসায় চোখ বুজিয়া ডাক্তারের হাতে আত্মসমর্পণ করে, তখন বিশ্বাস বস্তুটা একতরফাই থাকে! পীড়িতের বিশ্বাসের অনুরূপ জামিন ডাক্তারের কাছে কেহ দাবী করে না এবং করিলেও মেলে না। চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা, পারদর্শিতা, তাঁহার সাধু সদিচ্ছাই একমাত্র জামিন এবং সে তাঁহার নিছক নিজেরই হাতে। পরকে তাহা দেওয়া যায় না। রোগীকে বিশ্বাস করিতে হয় আপনারই কল্যাণে, আপনারই প্রাণ বাঁচাইবার জন্য।
এ পক্ষ হইতেও প্রত্যুত্তর হইতে পারে, ওটা উদাহরণেই চলে, বাস্তবে চলে না। কারণ অসঙ্কোচে আত্মসমর্পণ করিবারও জামিন আছে, কিন্তু তাহা ঢের বড়, এবং তাহা গ্রহণ করেন চিকিৎসকের হৃদয়ে বসিয়া ভগবান নিজে। তাঁর আদায়ের দিন যখন আসে, তখন না চলে ফাঁকি, না চলে তর্ক। তাই বোধ হয় সমস্ত ছাড়িয়া মহাত্মাজী রাজশক্তির এই হৃদয় লইয়াই পড়িয়াছিলেন। তিনি বোধ হয় সমস্ত ছাড়িয়া মহাত্মাজী রাজশক্তির এই হৃদয় লইয়াই পড়িয়াছিলেন। তিনি মারামারি, কাটাকাটি, অস্ত্রশস্ত্র, বাহুবলের ধার দিয়া যান নাই, তাঁর সমস্ত আবেদন-নিবেদন, অভিযোগ-অনুযোগ এই আত্মার কাছে।
রাজশক্তির হৃদয় বা আত্মার কোন বালাই না থাকিতে পারে, কিন্তু এই শক্তিকে চালনা যাহারা করে, তাহারাও নিষ্কৃতি পায় নাই। এবং সহানুভূতিই যখন জীবের সকল সুখ-দুঃখ, সকল জ্ঞান, সকল কর্মের আধার, তখন ইহাকেই জাগ্রত করিতে তিনি প্রাণপণ করিয়াছিলেন। আজ স্বার্থ ও অনাচারে ইহা যত মলিন, যত আচ্ছন্নই না হইয়া থাক্, একদিন ইহাকে নির্মল ও মুক্ত করিতে পারিবেন, এই অটল বিশ্বাস হইতে তিনি এক মুহূর্তও বিচ্যুত হন নাই। কিন্তু লোভ ও মোহ দিয়া স্বার্থকে, ক্রোধ ও বিদ্বেষ দিয়া হিংসাকে নিবারণ করা যায় না, তাহা মহাত্মা জানিতেন। তাই দুঃখ দিয়া নহে, দুঃখ সহিয়া, বধ করিয়া নহে, আপনাকে অকুণ্ঠিতচিত্তে বলি দিতেই এই ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইহাই ছিল তাঁহার তপস্যা, ইহাকে তিনি বীরের ধর্ম বলিয়া অকপটে প্রচার করিয়াছিলেন। পৃথিবীব্যাপী এই যে উদ্ধত অবিচারের জাঁতা-কলে মানুষ অহোরাত্র পিষিয়া মরিতেছে, ইহার একমাত্র সমাধান গুলি-গোলা, বন্দুক-বারুদ, কামানের মধ্যে নাই, আছে কেবল মানবের প্রীতির মধ্যে, তাঁহার আত্মার উপলব্ধির মধ্যে, এই পরম সত্যকে তিনি সমস্ত প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন বলিয়াই অহিংসা-ব্রতকে মাত্র ক্ষণেকের উপায় বলিয়া নয়, চিরজীবনের একমাত্র ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং এইজন্যেই তিনি ভারতীয় আন্দোলনকে রাজনীতিক না বলিয়া আধ্যাত্মিক বলিয়া বুঝাইবার চেষ্টায় দিনের পর দিন প্রাণপাত পরিশ্রম করিতেছিলেন। বিপক্ষ উপহাস করিয়াছে, স্বপক্ষ অবিশ্বাস করিয়াছে, কিন্তু কোনটাই তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই। ইংরাজ-রাজশক্তির প্রতি বিশ্বাস হারাইয়াছেন, কিন্তু মানুষ-ইংরাজদের আত্মোপলব্ধির প্রতি আজও তাঁহার বিশ্বাস তেমনি স্থির হইয়া আছে।
কিন্তু এই অচঞ্চল নিষ্কম্প শিখাটির মহিমা বুঝিয়া উঠা অনেকের দ্বারাই দুঃসাধ্য। তাই সেদিন শ্রীযুক্ত বিপিনবাবু যখন মহাত্মাজীর কথা—“I would decline to gain India’s Freedom at the cost of non-violence, meaning that India will never gain her Freedom without non-violence.” তুলিয়া ধরিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, ‘মহাত্মাজীর লক্ষ্য—সত্যাগ্রহ, ভারতের স্বাধীনতা বা স্বরাজলাভ এই লক্ষ্যের একটা অঙ্গ হইতে পারে, কিন্তু মূল লক্ষ্য নহে’, তখন তিনিও এই শিখার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। অপরের সম্পূর্ণ স্বাধীনতার প্রতি হস্তক্ষেপ না করিয়া মানবের পূর্ণস্বাধীনতা যে কত বড় সত্য বস্তু এবং ইহার প্রতি দ্বিধাহীন আগ্রহও যে কত বড় স্বরাজসাধনা, তাহা তিনিও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই! সত্যের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মূল ডাল প্রভৃতি নাই, সত্য সম্পূর্ণ এবং সত্যই সত্যের শেষ।
এবং এই চাওয়ার মধ্যেই মানবজাতির সর্বপ্রকার এবং সর্বোত্তম লক্ষ্যের পরিণতি রহিয়াছে। দেশের স্বাধীনতা বা স্বরাজ তিনি সত্যের ভিতর দিয়াই চাহিয়াছেন, মারিয়া কাটিয়া ছিনাইয়া লইতে চাহেন নাই, এমন করিয়া চাহিয়াছেন, যাহাতে দিয়া সে নিজেও ধন্য হইয়া যায়। তাহার ক্ষুব্ধ-চিত্তের কৃপণের দেয় অর্থ নয়, তাহার দাতার প্রসন্ন হৃদয়ের সার্থকতার দান। অমন কাড়াকাড়ির দেওয়া-নেওয়া ত সংসারে অনেক হইয়া গেছে, কিন্তু সে ত স্থায়ী হইতে পারে নাই,—দুঃখ কষ্ট বেদনার ভার ত কেবল বাড়িয়াই চলিয়াছে, কোথাও ত একটি তিলও কম পড়ে নাই! তাই তিনি আজ ও-সকল পুরাতন পরিচিত ও ক্ষণস্থায়ী অসত্যের পথ হইতে বিমুখ হইয়া সত্যাগ্রহী হইয়াছিলেন, পণ করিয়াছিলেন—মানবাত্মার সর্বশ্রেষ্ঠ দান ছাড়া হাত পাতিয়া আর তিনি কিছুই গ্রহণ করিবেন না।
সর্বান্তঃকরণে স্বাধীনতা বা স্বরাজকামী তিনি যখন ইংরেজ-রাজত্বের সর্বপ্রকার সংস্রব পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে বিস্তর কটুকথা শুনিতে হইয়াছিল। বহু কটূক্তির মধ্যে একটা তর্ক এই ছিল যে, ইংরাজ-রাজত্বের সহিত আমাদের চিরদিনের অবিচ্ছিন্ন বন্ধন কিছুতেই সত্য হইতে পারে না। নিরুপদ্রব শান্তির জন্যই বা এত ব্যাকুল হওয়া কেন? পরাধীনতা যখন পাপ এবং পরের স্বাধীনতা অপহরণকারীও যখন এতবড় পাপী, তখন যেমন করিয়া হউক, ইহা হইতে মুক্ত হওয়াই ধর্ম। ইংরাজ নিরুপদ্রব-পথে রাজ্যস্থাপন করে নাই, এবং রক্তপাতেও সংকোচ বোধ করে নাই, তখন আমাদেরই শুধু নিরুপদ্রবপন্থী থাকিতে হইবে, এতবড় দায়িত্ব গ্রহণ করি কিসের জন্য? কিন্তু মহাত্মাজী কর্ণপাত করেন নাই, তিনি জানিতেন, এ যুক্তি সত্য নয়, ইহার মধ্যে একটা মস্তবড় ভুল প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। বস্তুতঃ এ কথা কিছুতেই সত্য নয়, জগতে যাহা কিছু অন্যায়ের পথে, অধর্মের পথে একদিন প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেছে, আজ তাহাকে ধ্বংস করাই ন্যায়, যেমন করিয়া হোক তাহাকে বিদূরিত করাই আজ ধর্ম। যে ইংরাজ-রাজকে একদিন প্রতিহত করাই ছিল দেশের সর্বোত্তম ধর্ম, সেদিন তাহাকে ঠেকাইতে পারি নাই বলিয়া আজ যে -কোন পথে তাহাকে বিনাশ করাই দেশের একমাত্র শ্রেয়ঃ, এ কথা কোনমতেই জোর করিয়া বলা চলে না। অবাঞ্ছিত জারজ সন্তান অধর্মের পথেই জন্মলাভ করে, অতএব ইহাকে বধ করিয়াই ধর্মহীনতার প্রায়শ্চিত্ত করা যায়, তাহা সত্য নয়।
মহাত্মার পদত্যাগ
সংবাদ আসিয়াছে, মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের নেতৃত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন। খবরটা আকস্মিক নয়। কিছুদিন যাবৎ এমন একটা সম্ভাবনা বাতাসে ভাসিতেছিল, মহাত্মা রাজনীতির প্রবাহ হইতে আপনাকে অপসৃত করিয়া স্বীয় বিশাল ব্যক্তিত্ব, বিরাট কর্মশক্তি ও একাগ্রচিত্ত ভারতের আর্থিক নৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধানে নিয়োজিত করিবেন। তাহাই হইয়াছে। দেখা গেল, জাতীয় মহাসমিতির সভামণ্ডপে বহু কর্মী, বহু ভক্ত, বহু বন্ধুজনের আবেদন-নিবেদন অনুনয়-বিনয় তাঁহাকে সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। পারার কথাও নয়। বহুবার বহু বিষয়েই প্রমাণিত হইয়াছে, অশ্রুধারার প্রবলতা দিয়া কোনদিন মহাত্মাজীকে বিচলিত করা যায় না। কারণ, তাঁর নিজের যুক্তি ও বুদ্ধির বড় সংসারে আর কিছু আছে, বোধ হয় তিনি ভাবিতেই পারেন না। কিন্তু তাই বলিয়া এই কথাই বলি না, এ বুদ্ধি সামান্য বা সাধারণ। এ বুদ্ধি অসামান্য, অসাধারণ। অনুরাগিগণের ঢাকিয়া রাখার বহু চেষ্টা সত্ত্বেও এ বুদ্ধি তাঁহার কাছে অবশেষে এ সত্য উদ্ঘাটিত করিয়াছে যে, কংগ্রেসে তাঁহার প্রয়োজনীয়তা অন্ততঃ বর্তমানের জন্য শেষ হইয়াছে, অথচ বিস্ময় এই যে, তাঁহার দুঃসহ প্রভুত্বে যাঁহারা নিজেদের উৎপীড়িত লাঞ্ছিত জ্ঞান করিয়াছেন, মহাত্মার চিন্তা ও কার্যপদ্ধতির অনুধাবন করিতে পদে পদে যাঁহারা দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছেন, নেপথ্যে অনুযোগ-অভিযোগের যাঁহাদের অবধি ছিল না, তাঁহারাও সে কথা প্রকাশ্যে উচ্চারণ করিতে সাহস করেন নাই। বরঞ্চ, নানারূপে তাঁহার প্রসাদ-লাভের জন্য যত্ন করিয়া সেই নেতৃত্বেই তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার জন্য প্রাণপণ করিয়াছেন। বোধ করি শঙ্কা তাঁহাদের এই যে, এতবড় ভারতে নেতৃত্ব করিবার লোক আর তাঁহারা খুঁজিয়া পাইবেন না। কিন্তু খুঁজিয়া না পাওয়া গেলেও এ কথা বলিব যে, যেখানে স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন উক্তি, স্বাধীন অভিমত বারংবার প্রতিরুদ্ধ হইয়া জাতীয় মহাসমিতিকে পঙ্গুপ্রায় করিয়া আনিয়াছে, সেখানে মহাত্মার অথবা কাহারও নিরবচ্ছিন্ন সার্বভৌম আধিপত্য কল্যাণকর নয়।
আজ মহাত্মার মত, পথ ও যুক্তির আলোচনা করিব না। চরকায় দেশের অধোগতি প্রতিহত করিতে পারে কি না, বিদ্রোহ অসহযোগে দেশের রাজনৈতিক মুক্তি আনিতে পারে কি না, আইন-অমান্য আন্দোলনের শেষ পরিণাম কি, এ-সকল প্রশ্ন আজ থাক, কিন্তু মহাত্মার এ দাবী সত্য বলিয়াই স্বীকার করি যে, তাঁহার প্রবর্তিত পথে ভারত ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই।
একদিন কংগ্রেস আবেদন-নিবেদন অভিযোগ-অনুযোগের সুদীর্ঘ তালিকা প্রস্তুত করিয়াই নিজের কর্তব্য শেষ করিত। বঙ্গ-বিভেদের দিনেও জাতীয় মহাসমিতি বঙ্গকে তাহার অঙ্গ বলিয়া ভাবিতে জানিত না, বাঙলার প্রশ্ন ছিল শুধু বাঙলারই, বোম্বাই-অহমদাবাদ বাঙালীকে এক টাকার কাপড় চার টাকায় বিক্রি করিত, কংগ্রেস নিরুপায় বিস্মিত-চক্ষে শুধু চাহিয়া থাকিত,—কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন, অক্ষম জাতীয় মহাসমিতিকে নিজের অদম্য অকপট বিশ্বাসের জোরে সমগ্রতা আনিয়া দিলেন মহাত্মা, দিলেন শক্তি, সঞ্চারিত করিলেন প্রাণ, তাঁহার এই দানই সকৃতজ্ঞ-চিত্তে স্মরণ করিব। উত্তরকালে হয়ত তাঁহার মত ও পথ উভয়ই পরিবর্তিত হইবে, তাঁহার প্রবর্তিত আদর্শের হয়ত চিহ্নও থকিবে না, তথাপি তিনি যাহা দিয়া গেলেন, সমস্ত পরিবর্তনের মাঝেও তাহা অমর হইয়া রহিবে। শৃঙ্খলমুক্ত ভারত ঋণ তাঁহার কোনও দিন বিস্মৃত হইবে না। আজ কংগ্রেস-প্রতিষ্ঠানের তিনি বাহিরে আসিয়াছেন মাত্র, কিন্তু ইহাকে ত্যাগ করেন নাই, করিবার উপায় নাই। যে শিশুকে তিনি মানুষ করিয়াছেন, সে আজ বড় হইয়াছে। তাই তাহাকে নিজের কঠিন শাসনপাশ হইতে মহাত্মা স্বেচ্ছায় মুক্তি দিলেন। ইহাতে শোক করিবার কোন কারণ ঘটে নাই,—এই মুক্তিতে উভয়েরই মঙ্গল হইবে, এই আমার আশা। (‘কিশলয়’, ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৪৪)
মুসলিম সাহিত্য-সমাজ
মুসলিম সাহিত্য-সমাজের দশম বার্ষিক অধিবেশনে আমাকে আপনারা সভাপতি নির্বাচন করেছেন।ছেন মুসলিম সাহিত্য-সমাজ, তথাপি এই নির্বাচনের মধ্যে একটি পরম ঔদার্য আছে। আমি হিন্দু অথবা মুসলমান সমাজের অন্তর্গত ,আমি বহুদেবতাবাদী অথবা একেশ্বরবাদী এ প্রশ্ন আপনারা করেন নি। শুধু ভেবেছেন—আমি বাঙ্গালী, বঙ্গ-সাহিত্যের সেবায় প্রাচীন হয়েছি। অতএব, সাহিত্যিক দরবারে আমারও একটি স্থান আছে। সেই স্থানটি অকুণ্ঠচিত্তে আমাকে দিয়েছেন। আমিও আনন্দে সকৃতজ্ঞ মনে সেই দান গ্রহণ করেছি। ভাবি, সকল বিষয়েই আজ যদি এমনি হতে পারত! যে গুণী, যে মহৎ, যে বড়—সে হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, কৃশ্চান হোক, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য যা-ই হোক, স্বচ্ছন্দে সবিনয়ে তাঁর যোগ্য আসন তাঁকে দিতে পারতাম। সংশয়-দ্বিধা কোথাও কণ্টক রোপণ করতে পারতো না। কিন্তু যাক সে কথা। আমি পূর্বে একটি পত্রে বলেছিলাম, সাহিত্যের তত্ত্ব-বিচার অনেক হয়ে গেছে। অনেক মনীষী, অনেক রসিক, অনেক অধিকারী বহুবার এর সীমানা এবং স্বরূপ নির্দেশ করে দিয়েছেন, সে আলোচনা আর প্রবর্তন করার আমার রুচি নেই। আমি বলি সাহিত্য-সম্মিলন প্রবন্ধপাঠের জন্য নয়, সুতীক্ষ্ণ সমালোচনায় কাউকে ধরাশায়ী করার জন্য নয়, কে কত অক্ষম উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করার জন্য নয়, যে যা লিখেছে তার চেয়ে ভাল কেন লেখেনি, এ কৈফিয়ত আদায়ের জন্য নয়, এ শুধু সাহিত্যিকে সাহিত্যিকে মিলনক্ষেত্র। এর আয়োজন একের সঙ্গে অপরের ভাব-বিনিময় ও সম্যক পরিচয়ের জন্য। আমার মনে পড়ে, বয়স যখন অল্প ছিল, এ ব্রতে যখন নূতন ব্রতী, তখন আমন্ত্রণ পেয়েও কত সাহিত্য-সভায় দ্বিধায় সঙ্কোচে উপস্থিত হতে পারিনি, নিশ্চিত জানতাম সভাপতির সুদীর্ঘ অভিভাষণের একটা অংশ আমার জন্য নির্দিষ্ট আছেই। কখনও নাম দিয়ে, কখনও না দিয়ে। বক্তব্য অতি সরল। আমার লেখায় দেশ দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ হয়ে এলো এবং সনাতন হিন্দুসমাজ জাহান্নামে গেল বলে। যাবার আশঙ্কা ছিল, অসহিষ্ণু হয়ে যদি নজির দিয়ে আমি তার জবাব দিতাম। কিন্তু সে অপকর্ম কোনদিন করিনি—ভাবতাম, আমার সাহিত্য-রচনা যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, একদিন না একদিন লোকে বুঝবেই। যাই হোক, যে দুঃখ নিজে ভোগ করেছি, সে আর পরকে দিতে চাইনে। তবে অকপটে বলতে পারি, আমার অভিভাষণ শুনে সাহিত্যিক বিজ্ঞতা আপনাদের এক তিলও বাড়বে না, এবং বাড়বেই না যখন জানি, তখন কতকগুলো বাহুল্য কথার অবতারণা করি কেন? এইখানেই শেষ করলেই ত হত। হত না তা নয়, তবে নিজেই নাকি কথাটা একদিন তুলেছিলাম, তাই তারই সূত্র ধরে এই সম্মিলনে আরও গোটা-কয়েক কথা বলবার লোভ হয়।
একদিন আমার কলকাতার বাড়িতে কাজী মোতাহার সাহেব এসে উপস্থিত। সাহিত্য-আলোচনা করতে তিনি যাননি, গিয়েছিলেন দাবা খেলতে,—এ দোষ আমাদের উভয়েরই আছে—অসুস্থ ছিলাম, খেলা হল না, হল বর্তমান সাহিত্য প্রসঙ্গে দুটো আলোচনা। তারই মোটামুটি ভাবটা আমি কল্যাণীয়া জাহান্-আরার বার্ষিক পত্র ‘বর্ষবাণী’তে চিঠির আকারে লিখে পাঠাই। এবং সেইটি ‘অবাঞ্ছিত ব্যবধান’ শিরোনামায় ‘বুলবুল’ মাসিকপত্রের সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ মুহম্মদ হবিবুল্লাহ সাহেব উদ্ধৃত করেছেন তাঁর আষাঢ়ের কাগজে। দেখলাম, তার একটা জবাব দিয়েছেন শ্রীযুক্ত লীলাময় রায়, আর একটা দিয়েছেন ওয়াজেদ আলী সাহেব।
লীলাময়ের লেখার মধ্যে ক্ষোভ আছে, ক্রোধ আছে, নৈরাশ্য আছে। আমি বলেছিলাম, সাহিত্য-সাধনা যদি সত্য হয়, সেই সত্যের মধ্য দিয়েই ঐক্য একদিন আসবেই। কারণ, সাহিত্য-সেবকেরা পরস্পরের পরমাত্মীয়। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, কৃশ্চান হোক, তবু পর নয়—আপনার জন। লীলাময় বললেন, “প্রতিকার যদি থাকে, তবে তা সাহিত্যে নয়—তা স্বাজাত্যে”। স্বাজাত্য শব্দটায় তিনি কি বলতে চেয়েছেন, বুঝলাম না। বলেছেন, “ঐক্য জিনিসটা organic; হাড়ের সঙ্গে মাংস জুড়লে যেমন মানুষ হয় না, তেমনি হিন্দুর সঙ্গে মুসলমান জুড়লে বাঙ্গালী হয় না, ভারতীয় হয় না।” পরে বলেছেন, “হিন্দু-মুসলমানে আপস ছাড়া আর কিছু করবার নেই। সুতরাং ব্যবধান থেকে যাবে, জাতীয়তাও হবে না, আত্মীয়তাও না।” এ-সব উক্তি ক্ষোভের প্রকাশ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু বলি, এঁদের মতো শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক পণ্ডিত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও আজ যদি এই কথা বলতে থাকেন ত নৈরাশ্যে যে সমস্ত দিক কালো হয়ে উঠবে। এ কি এঁরা ভাবেন না? মনের তিক্ততা দিয়ে কোন মীমাংসাও হয় না, মিলনও ঘটে না। আবার এমনি হতাশা প্রকাশ পেয়েছে মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর প্রবন্ধে। তিনি বলেছেন, “আজ যাঁরা নূতন করে আমাদের দুই প্রতিবেশী সমাজের সম্বন্ধে বিচার করবেন, এ নিয়ে যে আশ্চর্য সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তার বন্ধন কেটে কল্যাণের অভিসারী হবেন, দীর্ঘ তাঁদের পথ, কঠিন তাঁদের সাধনা।” আমি এই কথাটাই মানতে চাইনে। জোর করে প্রশ্ন করতে চাই, কেন তাঁদের পথ দীর্ঘ হবে? কিসের জন্য সাধনা তাঁদের সুকঠিন হয়ে উঠবে? কেন একটি সহজ সুন্দর পথে এই সমস্যার সমাধান আমরা খুঁজে পাব না? ওয়াজেদ আলী সাহেব পরে বলেছেন, “যাদের মনে রইলো প্রবল বিরুদ্ধতা, অন্তরে রইলো গভীর অপ্রেম, চিত্তে রইলো দীর্ঘ ব্যবধান, তাদেরকে টেনে পাশাপাশি দাঁড় করানো হল।
তাতে শিষ্টাচারের তাগিদে হাতের সাথে হাত মিললো, তাদের দৃষ্টি-বিনিময় হল না; একজনের অন্তর রইলো আর একজনের অন্তর থেকে শত যোজন দূরে।” এর হেতু দেখাতে গিয়ে বলেছেন, “অচেনা মুসলিম এলো বিজয়ীর বেশে, অধিকার করলো রাজার আসন। আনুগত্য, রাজসম্মান সে পায়নি এমন নয়; কিন্তু ভারতবর্ষকে স্বদেশ স্বীকার করেও দেশ-মনের মিতালি তার ভাগ্যে হয়নি, এদের অপরিচয়ের যে ব্যবধান সেটি অবাঞ্ছিত হলেও কোনদিন ঘোচেনি।” কিন্তু এই কি সমস্ত সত্য? সত্য হলে, এই অবাঞ্ছিত ব্যবধান ঘুচিয়ে মিতালি করতে ক’টা দিন লাগে? মনে হয় লীলাময় অনেক ব্যথার মধ্যে দিয়েই লিখেছেন, “যাঁরা বিদেশ থেকে এসেছেন ও আজও তা মনে রেখেছেন, যাঁরা জলের উপর তেলের মত থাকবেন বলে স্থির করেছেন আবহমান কাল, দেশের অতীত সম্বন্ধে যাঁদের অনুসন্ধিৎসা ও বর্তমান সম্বন্ধে যাঁদের বেদনা-বোধ নেই, রাষ্ট্রের ভিতরে আর একটা রাষ্ট্র-রচনাই যাঁদের স্বপ্ন, আমরা তাঁদের কে, যে গায়ে পড়ে তাঁদের অপ্রিয় সত্য শোনাতে যাবো?”
এ কথার এ অর্থ নয় যে, ব্যবধান আমরা ভালবাসি, মিতালি চাইনে, পরস্পরের আলোচনা-সমালোচনা পরিহার করাই আমাদের বিধেয়। এ উক্তির তাৎপর্য যে কি, সমস্ত সাহিত্য-রসিক বিদগ্ধ মুসলিম সমাজকেই আমি দিতে বলি। কলহ-বিবাদ, তর্ক-বিতর্ক, বাদ-বিতণ্ডা করে নয়। কোথায় ভ্রম, কোথায় অন্যায়, কোন্খানে অবিচার লুকিয়ে আছে, সেই অকল্যাণকে সুস্থ সবল চিত্ত দিয়ে আবিস্কার করে দিতে বলি, এবং বলি উভয় পক্ষকেই সবিনয়ে সশ্রদ্ধায় তাকে স্বীকার করে নিতে। তখন পরস্পরের স্নেহ, প্রেম, ক্ষমা আমরা পাবোই পাবো।
ওয়াজেদ আলী সাহেব একটি চমৎকার ভরসার কথা বলেছেন, সেটি হিন্দু-মুসলমান সকলেরই মনে রাখা উচিত। বলেছেন, “মুসলিম সাহিত্য-সেবক আরবী-ফারসী শব্দ বাংলা ভাষার অঙ্গে জুড়তে চাইছেন, এতে আপত্তি-অনাপত্তি অতি তুচ্ছ কথা, কেননা শুধু কলম চালিয়ে ওটি হতে পারে না; তার জন্যে চাই প্রচুর সাহিত্যিক শক্তি, চাই সৃষ্টিশীল প্রতিভা। ও দুটি যেখানে নেই, সেখানে ভাষা ভূষণ পরতে গিয়ে অতি সহজেই সং সাজতে পারে।”
পারেই ত। কিন্তু এ জ্ঞান আছে কার? যিনি যথার্থ সাহিত্য-রসিক, তাঁর। ভাষাকে যিনি ভালবাসেন, অকপটে সাহিত্যের সেবা করেন, তাঁর। তাঁকে ত আমার ভয় নেই। আমার ভয় শুধু তাঁদের যাঁরা সাহিত্য-সেবা না করেও সাহিত্যের মুরুব্বি হয়ে বসেছেন। প্রিয় না হলেও একটা দৃষ্টান্ত দিই। ‘মহেশ’ নামে আমার লেখা একটি ছোট গল্প আছে, সেটি সাহিত্যপ্রিয় বহু লোকেরই প্রশংসা পেয়েছিল। একদিন শুনতে পেলাম গল্পটি Matric-এর পাঠ্য-পুস্তকে স্থান পেয়েছে। আবার একদিন কানে এলো সেটি নাকি স্থানভ্রষ্ট হয়েছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে নিজের কোন যোগ নেই, ভাবলাম এমনিই হয়ত নিয়ম। কিছুদিন থাকে, আবার যায়। কিন্তু বহুদিন পরে এক সাহিত্যিক বন্ধুর মুখে কথায় কথায় তার আসল কারণ শুনতে পেলাম। আমার গল্পটিতে নাকি গো-হত্যা আছে। আহা! হিন্দু বালকের বুকে যে শূল বিদ্ধ হবে! বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বহু টাকা মাইনের কর্তা-মশায় এ অনাচার সইবেন কি করে? তাই ‘মহেশ’, এর স্থানে শুভাগমন করেছেন তাঁর স্বরচিত গল্প ‘প্রেমের ঠাকুর’। আমার ‘মহেশ’ গল্পটা হয়ত কেউ কেউ পড়ে থাকবেন, আবার অনেকেই হয়ত পড়েন নি। তাই শুধু বিষয়-বস্তুটা সংক্ষেপে বলি। একটি হিন্দুপ্রধান হিন্দু জমিদার-পালিত ক্ষুদ্র গ্রামে গরীব চাষা গফুরের বাড়ি। বেচারার থাকার মধ্যে বহুজীর্ণ, বহুছিদ্রযুক্ত একখানি খড়ের ঘর, বছর-দশেকের মেয়ে আমিনা, আর একটি ষাঁড়। গফুর ভালবেসে তার নাম দিয়েছিল মহেশ। বাকি খাজনার দায়ে ছোট গাঁয়ের ততোধিক ছোট জমিদার যখন তার ক্ষেতের ধান-খড় আটক করলে, তখন সে কেঁদে বললে, হুজুর! আমার ধান তুমি নাও, বাপ-বেটীতে ভিক্ষে করে খাবো, কিন্তু খড় ক’টি দাও,—নইলে এ-দুর্দিনে মহেশকে আমার বাঁচাবো কি করে? কিন্তু রোদন তার অরণ্যে রোদন হল—কেউ দয়া করলে না। তার পরে শুরু হল তার কত রকমের দুঃখ, কত রকমের উৎপীড়ন। মেয়ে জলের জন্যে বাইরে গেলে সেই জীর্ণ কুটীরের খড় ছিঁড়ে নিয়ে লুকিয়ে মহেশকে খাওয়াতো, মিছে করে বলতো, মা আমিনা, আজ আমার জ্বর হয়েছে, আমার ভাত ক’টি তুই মহেশকে দে। সারাদিন নিজে অভুক্ত থাকতো। ক্ষুধার জ্বালায় মহেশ অত্যাচার করলে এই দশ বছরের মেয়েটার কাছেও তার ভয় ও কুণ্ঠার অবধি থাকতো না। লোকে বলতো, গরুটাকে তুই খাওয়াতে পারিস নে গফুর, ওকে বেচে দে। গফুর চোখের জল ফেলে আস্তে আস্তে তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলতো, মহেশ, তুই আমার ব্যাটা,—আমাকে তুই সাত সন প্রতিপালন করেছিস। খেতে না পেয়ে তুই কত রোগা হয়ে গেছিস,—তোকে কি আজ আমি পরের হাতে দিতে পারি, বাবা! এমনি করে দিন যখন আর কাটতে চায় না তখন একদিন অকস্মাৎ এক বিষম কাণ্ড ঘটলো। সে গ্রামে জলও সুলভ নয়। শুকনো পুকুরের নীচে গর্ত কেটে সামান্য একটুখানি পানীয় জল বহু দুঃখে মেলে। আমিনা দরিদ্র মুসলমানের মেয়ে, ছোঁয়া-ছুঁইর ভয়ে পুকুরের পাড়ে, দূরে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশী মেয়েদের কাছে চেয়ে-চিন্তে অনেক দুঃখে বিলম্বে তার কলসীটি পূর্ণ করে বাড়ি ফিরে এলো। এখন ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত মহেশ তাকে ফেলে দিয়ে কলসী ভেঙ্গে ফেলে এক নিশ্বাসে মাটি থেকে জল শুষে খেতে লাগলো।
মেয়ে কেঁদে উঠলো। জ্বরগ্রস্ত, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ গফুর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো—এ দৃশ্য তার সইলো না। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যা সুমুখে পেলে—একখণ্ড কাঠ দিয়ে সবলে মহেশের মাথায় মেরে বসলো। অনশনে মৃতকল্প গরুটা বার-দুই হাত-পা ছুঁড়ে প্রাণত্যাগ করলে।
প্রতিবাসীরা এসে বললে, হিন্দুর গাঁয়ে গোহত্যা! জমিদার পাঠিয়েছেন তর্করত্নের কাছে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নিতে। এবার তোর ঘরদোর না বেচতে হয়। গফুর দুই হাঁটুর ওপর মুখ রেখে নিঃশব্দে বসে রইলো। মহেশের শোকে, অনুশোচনায় তার বুকের ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছিলো। অনেক রাতে গফুর মেয়েকে তুলে বললে, চল্ আমরা যাই।
মেয়ে দাওয়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিল, চোখ মুছে বললে, কোথায় বাবা? গফুর বললে, ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে।
আমিনা আশ্চর্য হয়ে চেয়ে রইলো। ইতিপূর্বে অনেক দুঃখেও তার বাবা চটকলে কাজ করতে রাজী হয়নি। বাবা বলতো, ওখানে ধর্ম থাকে না, মেয়েদের আব্রু-ইজ্জত থাকে না—ওখানে কখন নয়। কিন্তু হঠাৎ এ কি কথা?
গফুর বললে, দেরি করিস নে মা, চল্। অনেক পথ হাঁটতে হবে। আমিনা জল খাবার পাত্র এবং বাবার ভাত খাবার পিতলের বাসনটি সঙ্গে নিতেছিল, কিন্তু বাবা বারণ করে বললে, ও-সব থাক্ মা, ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে।
তার পরে গল্পের উপসংহারে বইয়ে এইরূপ আছে—“অন্ধকার গভীর নিশীথে সে মেয়ের হাত ধরিয়া বাহির হইল। এ গ্রামে আত্মীয় কেহ তাহার ছিল না, কাহাকেও বলিবার কিছু নাই। আঙ্গিনা পার হইয়া পথের ধারে সেই বাবলা-তলায় আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, আল্লাহ! আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখেনি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি কখনো যেন মাফ্ করো না।”
এই হল গোহত্যা! এই পড়ে হিন্দুর ছেলের বুকে শেল বিঁধবে। তার চেয়ে পড়ুক ‘প্রেমের ঠাকুর’! তাতে ইহলোক না হোক তাদের পরলোকে সদ্গতি হবে! এই কান্তিমান সুপরিপুষ্ট প্রেমের ঠাকুরটিকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে, মুসলমান-সম্পাদিত কাগজে এই গল্পটির যে কড়া আলোচনা বেরিয়েছিল তার কি কোন হেতু নেই? একেবারে মিথ্যা অমূলক?
তাই আমার চেয়েও বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটিকে সসম্মানে নিবেদন করে রাখি যে, খুব বড় হলেও মনের মধ্যে একটুখানি বিনয় থাকা ভাল। ভাবা উচিত, তাঁর রচিত গল্পের সঙ্গে বাঙলার ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচয় না ঘটলেও বিশেষ কোন লোকসান ছিল না। Text Book থেকে পয়সা পাইনে—ও ব্যবসা আমার নয়—সুতরাং ক্ষতিবৃদ্ধিও নেই—তবু ক্লেশবোধ হয়। নিজের জন্য নয়,—অন্য কারণে। শুধু সান্ত্বনা এই যে, অযোগ্যের হাতে ভার পড়লে এমনি দুর্দশাই ঘটে। যে ব্যক্তি কোনদিন সাহিত্য সাধনা করেনি সে কি করে বুঝবে কার মানে কি! শুনেছি নাকি আমার ‘রামের সুমতি’ গল্পের খানিকটা দিয়েছেন। অত্যন্ত দয়া,—বোধ করি আশা এর থেকে রামেদের সুমতি হবে। কিন্তু মুশকিল এই যে, দেশে রহিমরাও আছে।
আর শুধু বিদ্যালয়ই নয়, মহেশের ভাগ্যে অন্য দুর্ঘটনাও ঘটেছে। তার বিস্তারিত বিবরণ দিতে চাইনে, কিন্তু নিঃসংশয়ে জানি এক হিন্দু জমিদার রক্তচক্ষু হয়ে শাসিয়ে বলেছিলেন, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সাহায্যে ছাপা মাসিক বা সাপ্তাহিকে এ ধরনের গল্প যেন আর ছাপা না হয়। এতে জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজা ক্ষেপিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ দেশের সর্বনাশ হয়।
যাক নিজের কথা।
উপরি-উক্ত হিন্দু মুরব্বীর মত আবার মুসলমান মুরব্বীও আছেন। শুনেছি তাঁরা নাকি আদেশ করেন ইতিহাস ফরমায়েশ মত লিখতে। ইসলাম-ধর্মী কোন ব্যক্তি কোথাও অন্যায়-অবিচার করেছেন এর লেশমাত্রও যেন কোন পড়ার বইয়ে না থাকে। এখানেও সান্ত্বনা এই যে, এঁদের কেউ কখনো কোনকালে সাহিত্য-সেবা করেন নি। করলে এমন কথা মুখে আনতে পারতেন না। সত্যিকার সাহিত্যিকদের হাতে যদি এই ভার পড়ে, আমার বিশ্বাস, না-হিন্দু, না-মুসলিম কোন পক্ষ থেকেই বিন্দুমাত্র অভিযোগ শোনা যাবে না। ভাষার প্রতি, সাহিত্যের প্রতি সত্যিকার দরদ তাঁদের সত্য পথেই পরিচালিত করবে।
ওয়াজেদ আলী সাহেব এক স্থানে বলেছেন, “মুসলিমের এই নবস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ, ইসলামী কৃষ্টির এই বলিষ্ঠ জাগরণ, সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের মত শক্তিমান প্রতিভার মনোযোগ আকর্ষণ করলো, হয়ত দেশের অনাগত কল্যাণের এ এক শুভ ইঙ্গিত। কিন্তু তবু কেন মন সন্দেহ-অবিশ্বাসে দ্বিধা-জিজ্ঞাসায় দুলে ওঠে? ‘বুলবুলে’ প্রকাশিত তাঁর পত্রখানিতে যেন চোখে পড়ে, মুসলিমের প্রতি তাঁর সহানুভূতির অভাব, ভালবাসার অভাব এবং মোটামুটি একটা অন্তর্দৃষ্টির অভাব।”
আমার জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করে, মুসলিমের এই ‘নবস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ,’ ইসলামী কৃষ্টির এই ‘বলিষ্ঠ জাগরণ’, যাঁরা নবীন, উদার বাংলা ভাষাকে যাঁরা অকুণ্ঠিত মনে মাতৃভাষা বলে স্বীকার করেন, তাঁদের—না যাঁরা পুরাতনপন্থী, তাঁদের? আমার অভিমত এই যে, যাঁরা প্রাচীনপন্থী, যাঁরা পিছনে ছাড়া সুমুখে চাইতে জানেন না, তাঁদের জাগরণ, কি মুসলিম কি হিন্দু, সকল সমাজেরই বিঘ্নস্বরূপ। হিন্দুদের সম্বন্ধে এ কথা আমি বহুবার বহুস্থানে লিখেছি, মুসলিম-সমাজের সম্বন্ধেও অসংশয়ে বলতে পারি, এ জাগরণ হয় যদি নবীনের—আসুক সে শ্রাবণের পূর্ণিমা জোয়ারের মত সমস্ত ভাসিয়ে দিয়ে, তবু তাকে আমি দু-হাত তুলে সংবর্ধনা করে নেবো। জানবো, এদের হাতে সমস্তই হবে শুভ এবং সুন্দর—এদের হাতে হিন্দু-মুসলিম কারও ভয় নেই—এদের হাতে আমরা দুজনেই হবো নিরাপদ। আমার আশঙ্কা শুধু প্রাচীনপন্থীদের সম্বন্ধে।
তিনি পরে বলেছেন, “ শরৎচন্দ্রের মত সাহিত্যিকদের সম্প্রদায়, জাতি, এক ছাড়া দুই নয়। এ কথা সহজেই আমাদের স্বীকৃতি দাবী করতে পারে। কিন্তু আরও একটি সহজ কথার দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। সেটি এই যে সাহিত্য মানুষের মনের সৃষ্টি, এবং মানুষের মনকে তৈরী করে তার ধর্ম, তার সমাজ, তার পরিবেশ, তার কৃষ্টি। এদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা কি সামান্য ব্যাপার? এবং সাধারণতঃ সেটি কি সম্পূর্ণরূপে সম্ভব?”
এই কথাগুলি শুধু আংশিক সত্য—সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ, এটুকু মোটামুটি জেনে রাখা দরকার যে মানুষ যখন সাহিত্যরচনায় নিবিষ্ট-চিত্ত তখন সে ঠিক হিন্দুও নয়, মুসলিমও নয়। তখন সে তার সর্বজনপরিচিত, ‘আমি’টাকে বহু দূরে অতিক্রম করে যায়, নইলে তার সাহিত্যসাধনা ব্যর্থ হয়। এই জন্যেই যেখানে কিছুই এক নয়, বাহ্যতঃ কিছুই মেলে না, সেখানেও ম্যাক্সিম গর্কির মত সাহিত্য-সেবকেরা আমাদের বুকের মধ্যে অনেকখানি আত্মীয়ের আসন-জুড়ে বসে থাকেন। এই কথাটি আমি সকল সাহিত্যিককেই মনে রাখতে বলি। কে কোথায় তার অসতর্ক মুহূর্তে কি কথা বলেছে, সেইটিই তার জীবনের পরম সত্য নয়। কেবল তাই দিয়েই বিচার করা চলে না। এবং এই জন্যই ওয়াজেদ আলী সাহেব তাঁর প্রবন্ধে আমার সম্বন্ধে যে-সব কঠিন উক্তি করেছেন আমি তার জবাব দিতে বসবো না। রাগ যখন পড়বে, তখন আপনিই মনে হবে আমি সত্যি কথাই বলেছিলাম। ওয়াজেদ আলী সাহেব সবচেয়ে মর্মান্তিক কথা বলেছেন এইখানে, “বস্তুতঃ, দুইটি বিষম অনাত্মীয় কৃষ্টির সংঘর্ষের ফলে এই বিক্ষোভ। এর জন্য আক্ষেপ বৃথা। হিন্দু মুসলিমকে বোঝে না, এজন্যে দুঃখের বিলাপ আজ চারিদিকে ধ্বনিত হচ্ছে।
কিন্তু এমনও হতে পারে যে তার ভারতীয় ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতি তার মনকে-করেছে অপরিসর, দৃষ্টিকে করেছে আচ্ছন্ন।আপনার পরিধিকে অতিক্রম করে গতি তার নিশ্চল; আপনার আভিজাত্যের গর্বে যে চিরবিলীন, পরাজয়ের প্রাচীন অভিমান যার আজও দুর্জয়, বিনাযুদ্ধে সুচ্যগ্র-পরিমিত স্থান দান করতেও যার আপত্তি অন্তহীন, তার বুদ্ধিকে মুক্ত বলা কঠিন। অথচ, মুক্তি যার নেই সে চলে না, চলতে পারে না, সে জড়। এই আত্মকেন্দ্রী পরবিমুখ জড়বুদ্ধির পরিবেশ এ দেশের মুসলিমকে ‘নিজ বাসভূমে পরবাসী’ করে রেখেছে, ভারতের মাটির রসে রসায়িত হয়েও তার মন যেন ভিজছে না।”
এই যে বলেছেন দুইটি বিষম অনাত্মীয় কৃষ্টির ফলে এই বিক্ষোভ, এর জন্য আক্ষেপ বৃথা। আমরা উভয়ে উভয়ের প্রতিবেশী, আমাদের আকাশ বাতাস মাটি জল এক। মাতৃভাষা এক বলেই স্বীকার করি। তবু সংঘর্ষ এত বড় কঠোর যে, তার জন্যে আক্ষেপ পর্যন্ত করা বৃথা—এই মনোভাবই যদি সমস্ত হিন্দু-মুসলমানের সত্য হয় ত এই কথাই বলবো যে, এর চেয়ে বড় দুর্গতি মানুষের আর ঘটতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধিও কি জড়বুদ্ধি? মন তাঁর মুক্ত হয়নি? এ যদি সত্য তবে ওয়াজেদ আলী সাহেবের এ ভাষা এল কোথা থেকে? সহজ, সুন্দর ও অবলীলায় আপন মনোভাব প্রকাশ করার শক্তি তাঁকে কে দিলে? এ যুগে এমন লেখক, এমন সাহিত্য-সেবক কে আছে যে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী নয়? সাহিত্য ধর্ম-পুস্তকও নয়, নীতিশিক্ষার বইও নয়, অথচ, আপন বিশাল পরিধির মধ্যে আপন মাধুর্যে সে সব-কিছুকেই আপন করে রেখেছে। তাই সাহিত্য কি, রসবস্তু কি, আজও কেউ তার সত্য নির্দেশ পেলে না। কত তর্ক, কত মতভেদ। এই অবাঞ্ছিত ব্যবধান সম্বন্ধে মীজানুর রহমান সাহেব জ্যৈষ্ঠের ‘বুলবুল’ মাসিক পত্রে তাঁর প্রবন্ধের এক স্থানে অকরুণ হয়ে বলেছেন, “শরৎবাবু তাঁর রাশিকৃত উপন্যাসের ভিতর স্থানে স্থানে মুসলমান-সমাজের যে-সব ছবি এঁকেছেন তা মুসলমান-সমাজের খুব উঁচুদরের লোকের নয়।” কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, উঁচু-নিচু স্তরের পাত্র-পাত্রীর উপরেই কি উপন্যাসের উচ্চতা-নীচতা, ভাল-মন্দ নির্ভর করে? এ যদি তাঁর অভিমত হয়, তবে আমার সঙ্গে তাঁর মতের ঐক্য হবে না। না হোক, কিন্তু উপসংহারে যে বলেছেন, “হিন্দু-সমাজের বিবিধ গলদ ও সমস্যা নিয়ে শরৎচন্দ্র যে-সকল গল্প ও উপন্যাস লিখেছেন এবং প্রতিকারের উদ্দেশ্যে তাঁহার সমাজকে যে চাবুক কশেছেন, সদিচ্ছাপ্রণোদিত এমনধারা নির্মম কশাঘাতও মুসলিম-সমাজ অম্লানবদনে গ্রহণ করবে তা জোর করে বলতে পারি। বাঙ্গালার কথাসাহিত্য-সম্রাটকে একবার পরীক্ষা করে দেখতে অনুরোধ করি।”
সেদিন জগন্নাথ হলে আমার অভিনন্দনের প্রতিভাষণে এ কথার উত্তর দিয়েছি। অন্তরের শুভ-কামনাকে এঁরা কেমন করে গ্রহণ করেন, এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেবার পূর্বে আমি দেখে যাবো। সে যাই হোক, মানুষে শুধু ইচ্ছা প্রকাশ করতেই পারে, কিন্তু তার পরিপূর্ণতার ভার থাকে আর একজনের ’পরে, যিনি বাক্য ও মনের অগোচর।
সেদিন খেতে বসে His Excellency আমাকে এই প্রশ্নই করেছিলেন। আমি উত্তর দিয়াছিলাম, আমার সঙ্কল্প কাজে পরিণত করতে—চাই উভয় সমাজের আশীর্বাদ। ঠিক সমাজ নয়,— চাই উভয় সমাজের সাহিত্য-সেবকদের আশীর্বাদ। যে ভাষার যে সাহিত্যের এতকাল সেবা করেছি, তার ’পরে অকারণ অনাচার আমার সয় না। আমার একান্ত মনের বিশ্বাস, আমার মত সাহিত্যের যথার্থ সাধনা যাঁরা করেছেন, তাঁরা হিন্দু-মুসলিম যা-ই হোন, কারোও এ অনাচার সইবে না। সৌন্দর্য ও মাধুর্যের জন্য পরিবর্তন যদি কিছু কিছু প্রয়োজন হয়—এমন ত কতবার হয়েছে—সে কাজ ধীরে ধীরে এঁরাই করবেন। আর কেউ নয়। সে হিন্দুয়ানির কল্যাণেও নয়, মুসলমানির কল্যাণেও নয়—শুধু মাতৃভাষা ও সাহিত্যের কল্যাণে। এই আমার ছোট আবেদন।
কোথায় কোন্ লেখায় মুসলিম-সমাজের প্রতি অবিচার করেছি,— করিনি বলেই আমার ধারণা—তার চুলচেরা বাদ-প্রতিবাদ প্রতিকারের পথ নয়, সে কলহ-বিবাদের নতুন রাস্তা তৈরি করা।
‘বুলবুল’ কাগজখানির নানা স্থান থেকে আমি উদ্ধৃত করেছি—প্রয়োজনবোধে। এই পত্রিকার অবিচ্ছিন্ন উন্নতি কামনা করি, কারণ যতটুকু পড়েছি তাতে সাহিত্যের উন্নতিই এঁদের কাম্য, আমারও তাই। হয়ত কোথাও একটু কটূক্তি করে থাকবেন কিন্তু সে মনে করে রাখবার বস্তু নয়, ভুলে যাবার জিনিস।
কিন্তু আর নয়। বলবার বিষয় এখনও অনেক ছিল, কিন্তু আপনাদের ধৈর্যের প্রতি সত্যিই অত্যাচার করেছি। সেজন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করি। এ অভিভাষণে পাণ্ডিত্য নেই, কারুকার্য নেই, বলার কথাগুলো কেবল সোজা করে বলে গেছি, যেন তাৎপর্য বুঝতে কারও ক্লেশবোধ না হয়। শোনার পরে কেউ না বলেন—যেমন অতুলনীয় শব্দসম্পদ, তেমনি কারুকার্য—কিন্তু ঠিক কি যে বলা হল ভাল বোঝা গেল না।
বাংলা-সাহিত্যের সেবা করে মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা আমার অপরিসীম, তবু তাঁদের নামোল্লেখ করতে আমি বিরত রইলাম।
পরিশেষে কৃতজ্ঞতা নিবেদনের একটা রীতি আছে। যেমন আছে আরম্ভ করার সময় বিনয় প্রকাশের প্রথা। প্রথমটা করিনি। কারণ, সাহিত্য-সভায় সভাপতির কাজ এত বেশি করতে হয়েছে যে, এই ষাট বছর বয়সে নিজেকে অনুপযুক্ত, বেকুফ ইত্যাদি যত প্রকারের বিনয়সূচক বিশেষণ আছে নিজের নামের সঙ্গে সংযোগ করে দিলে ঠিক শোভন হবে মনে হল না। কিন্তু কৃতজ্ঞতা-প্রকাশের বেলায় তা নয়। সমস্ত বিদগ্ধ মুসলিম-সমাজের কাছে আজ আমি অকপটে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। আপনারা আমার সালাম গ্রহণ করুন। বলার দোষে যদি কাউকে বেদনা দিয়ে থাকি সে আমার ভাষার ত্রুটি, আমার অন্তরের অপরাধ নয়।
ইতি—ঢাকা, ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৪৩।
যুব-সঙ্ঘ
কল্যাণীয় ‘বেণু’র কিশোর-কিশোরী পাঠকগণ,—উত্তরবঙ্গের রংপুর শহর থেকে তোমাদের এইখানি লিখছি। তোমরা জান বোধ হয়, বাঙলাদেশে যুব-সমিতি নাম দিয়ে একটি সঙ্ঘের সৃষ্টি হয়েছে। হয়ত, আজও তোমরা এর সভ্যশ্রেণীভুক্ত নও, কিন্তু একদিন এই সমিতি তোমাদের হাতে এসেই পড়বে। তোমরাই এর উত্তরাধিকারী। তাই, এ সম্বন্ধে দুটো কথা তোমাদের জানিয়ে রাখতে চাই। সমিতির বার্ষিক সম্মিলনী কাল শেষ হয়ে গেছে। আমি বুড়োমানুষ, তবুও ছেলেমেয়েরা আমাকেই এই সম্মিলনীর নেতৃত্ব করবার জন্য আমন্ত্রণ করে এনেছে। তারা আমার বয়সের খেয়াল করেনি। কারণ বোধ করি এই যে, কেমন করে যেন তারা বুঝতে পেরেছে, আমি তাদের চিনি। তাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষার কথাগুলোর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আমি তাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে আনন্দের সঙ্গে ছুটে এসেছিলাম শুধু এই কথাটাই জানাতে যে, তাদের হাতেই দেশের সমস্ত ভালমন্দ নির্ভর করে, এই সত্যটা যেন তারা সকল অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করে। অথচ, এই পরম সত্যটাকে বোঝবার পথে তাদের কতই না বাধা। কত আবরণই না তৈরী হয়েছে তাদের দৃষ্টি থেকে একে ঢেকে রাখবার জন্যে। আর তোমরা, যাদের বয়স আরও কম, তাদের বাধার ত আর অন্ত নেই। বাধা যারা দেয়, তারা বলে, সকল সত্য সকলের জানবার অধিকার নেই। এই যুক্তিটা এমনি জটিল যে, না বলে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দেওয়াও যায় না, হাঁ বলেও সম্পূর্ণ মেনে নেওয়া যায় না। আর এইখানেই তাদের জোর। কিন্তু এমন করে এ বস্তুর মীমাংসা হয় না। হয়ও নি। সর্বদেশে, সর্বকালে প্রশ্নের পরে প্রশ্ন এসেছে;—অধিকার ভেদে তর্ক উঠেছে। শেষে বয়স ছেড়ে মানুষের ছোটবড়, উঁচুনীচু অবস্থার দোহাই দিয়ে মানুষকে মানুষ জ্ঞানের দাবী থেকেও বঞ্চিত করে রেখেছে।
তোমরাও এমনি তোমাদের জন্মভূমি সম্বন্ধে অনেক তথ্য অনেক জ্ঞান থেকেই বঞ্চিত হয়ে আছ। সত্য সংবাদ পেলে পাছে তোমাদের মন বিক্ষিপ্ত হয়, পাছে তোমাদের ইস্কুল-কলেজের পড়ায়, পাছে তোমাদের এক্জামিনে পাসের পরম বস্তুতে আঘাত লাগে, এই আশঙ্কায় মিথ্যে দিয়েও তোমাদের দৃষ্টিরোধ করা হয়, এ খবর হয়ত তোমরা জানতেও পার না।
যুব-সমিতির সম্মিলনে এই কথাটাই আমি সকলের চেয়ে বেশী করে বলতে চেয়েছিলাম। বলতে চেয়েছিলাম, তোমাদের পরাধীন দেশটিকে বিদেশীর শাসন থেকে মুক্তি দেবার অভিপ্রায়েই তোমাদের সঙ্ঘ গঠন। ইস্কুল-কলেজের ছাত্রদের পাঠ্যাবস্থাতেও দেশের কাজে যোগ দেবার—দেশের স্বাধীনতা-পরাধীনতার বিষয় চিন্তা করবার অধিকার আছে। এবং এই অধিকারের কথাটাও মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করবার অধিকার আছে।
বয়স কখনও দেশের ডাক থেকে কাউকে আটকে রাখতে পারে না, তোমাদের মত কিশোর-বয়স্কদেরও না।
এক্জামিনে পাস করা দরকার,—এ তার চেয়েও বড় দরকার। ছেলেবেলায় এই সত্যচিন্তা থেকে আপনাকে পৃথক করে রাখলে যে ভাঙ্গার সৃষ্টি হয়, একদিন বয়স বাড়লেও আর তা জোড়া লাগতে চায় না। এই বয়সের শেখাটাই সবচেয়ে বড় শিক্ষা। একেবারে রক্তের সঙ্গে মিশে যায়।
নিজেও ত দেখি, ছেলেবেলায় মায়ের কোলে বসে একদিন যা শিখেছিলাম, আজ এই বৃদ্ধ বয়সেও তা তেমনি অক্ষুণ্ণ আছে। সে শিক্ষার আর ক্ষয় নাই।
তোমরা নিজের বেলাতেও ঠিক তাই মনে করো। ভেবো না যে, আজ অবহেলায় যেদিকে দৃষ্টি দিলে না, আর একদিন বড় হয়ে তোমরা ইচ্ছামতই দেখতে পাবে। হয়ত পাবে না, হয়ত সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও সে দুর্লভ বস্তু চিরদিনই চোখের অন্তরালে রয়ে যাবে। যে শিক্ষা পরম শ্রেয়ঃ তাকে এই কিশোর বয়সেই শিরায় রক্তের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করে গ্রহণ করতে হয়, তবেই যথার্থ করে পাওয়া যায়। কালকের এই যুব-সমিতির যুবকেরা কংগ্রেসের ধরণ-ধারণ ছেলেবেলাতেই গ্রহণ করেছিল বলে সে রীতি-নীতি আর ত্যাগ করতে পারেনি। এটা ভয়ের কথা।
রংপুর, ১৭ চৈত্র, (১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, বৈশাখ-৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ‘বেনু’ মাসিকপত্রে প্রকাশিত)
রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে মানপত্র
কবিগুরু,
তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই।
তোমার সপ্ততিতম-বর্ষশেষে একান্তমনে প্রার্থনা করি, জীবন-বিধাতা তোমাকে শতায়ু দান করুন; আজিকার এই জয়ন্তী-উৎসবের স্মৃতি জাতির জীবনে অক্ষয় হউক।
বাণীর দেউল আজি গগন স্পর্শ করিয়াছে। বঙ্গের কত কবি, কত শিল্পী, কত না সেবক ইহার নির্মাণকল্পে দ্রব্যসম্ভার বহন করিয়া আনিয়াছেন। তাঁহাদের স্বপ্ন ও সাধনার ধন, তাঁহাদের তপস্যা তোমার মধ্যে আজি সিদ্ধিলাভ করিয়াছে। তোমার পূর্ববর্তী সেই সকল সাহিত্যাচার্যাগণকে তোমার অভিনন্দনের মাঝে অভিনন্দিত করি।
আত্মার নিগূঢ় রস ও শোভা, কল্যাণ ও ঐশ্বর্য তোমার সাহিত্যে পূর্ণ বিকশিত হইয়া বিশ্বকে মুগ্ধ করিয়াছে। তোমার সৃষ্টির সেই বিচিত্র ও অপরূপ আলোকে স্বকীয়-চিত্তের গভীর ও সত্য পরিচয়ে কৃত-কৃতার্থ হইয়াছি।
হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।
হে সার্বভৌম কবি, এই শুভ দিনে তোমাকে শান্তমনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি নতশিরে বারংবার নমস্কার করি।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১১ই পৌষ, ১৩৩৮।
রস-সেবায়েৎ
শ্রীযুক্ত ‘আত্মশক্তি’-সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,—
আপনার ৩০ শে ভাদ্রের ‘আত্মশক্তি’ কাগজে মুসাফির-লিখিত ‘সাহিত্যের মামলা’ পড়িলাম। একদিন বাংলা-সাহিত্যে সুনীতি-দুর্নীতির আলোচনায় কাগজে কাগজে অনেক কঠিন কথার সৃষ্টি হইয়াছে, আর অকস্মাৎ আজ সাহিত্যের ‘রসে’র আলোচনায় তিক্ত রসটাই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এমনিই হয়। দেবতার মন্দিরে সেবকের পরিবর্তে ‘সেবায়েতে’র সংখ্যা বাড়িতে থাকিলে দেবীর ভোগের বরাদ্দ বাড়ে না, কমিয়াই যায়, এবং মামলা ত থাকেই।
আধুনিক সাহিত্যসেবীদের বিরুদ্ধে সম্প্রতি বহু কুবাক্য বর্ষিত হইয়াছে। বর্ষণ করার পুণ্যকর্মে যাঁহারা নিযুক্ত, আমিও তাঁহাদের একজন। ‘শনিবারের চিঠি’র পাতায় তাহার প্রমাণ আছে।
মুসাফির-রচিত এই ‘সাহিত্যের মামলা’র অধিকাংশ মন্তব্যের সহিতই আমি একমত, শুধু তাঁহার একটি কথায় যৎকিঞ্চিৎ মতভেদ আছে।
রবীন্দ্রনাথের ব্যাপার রবীন্দ্রনাথ জানেন, কিন্তু আমার নিজের কথা যতটা জানি তাহাতে শরৎচন্দ্র ‘কল্লোল’, ‘কালি-কলম’ বা বাংলার কোন কাগজই পড়েন না বা পড়িবার সময় পান না, মুসাফিরের এ অনুমানটি নির্ভুল নয়। তবে, এ কথা মানি যে, সব কথা পড়িয়াও বুঝি না, কিন্তু না-পড়িয়াও সব বুঝি, এ দাবী আমি করি না।
এ ত গেল আমার নিজের কথা। কিন্তু যা লইয়া বিবাদ বাধিয়াছে সে জিনিসটি যে কি, এবং যুদ্ধ করিয়া যে কিরূপে তাহার মীমাংসা হইবে সে আমার বুদ্ধির অতীত।
রবীন্দ্রনাথ দিলেন সাহিত্যের ধর্ম নিরূপণ করিয়া, এবং নরেশচন্দ্র দিলেন সেই ধর্মের সীমানা নির্দেশ করিয়া। যেমন পাণ্ডিত্য তেমনই যুক্তি, পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ভাবিলাম, ব্যস্, ইহার পরে আর কথা চলিবে না। কিন্তু অনেক কথাই চলিল। তখন কে জানিত কাহার সীমানায় কে পা বাড়াইয়াছে এবং সেই সীমানার চৌহদ্দি লইয়া এত লাঠি-ঠ্যাঙ্গা উদ্যত হইয়া উঠিবে। আশ্বিনের ‘বিচিত্রা’য় শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী মহাশয় ‘সীমানা বিচারে’র রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ঠাসবুনানি বিশ পৃষ্ঠাব্যাপী ব্যাপার।
কত কথা, কত ভাবা! যেমন গভীরতা, তেমনি বিস্তৃতি, তেমনি পাণ্ডিত্য। বেদ, বেদান্ত, ন্যায়, গীতা, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কালিদাসের ছড়া, উজ্জ্বল-নীলমণি, মায় ব্যাকরণের অধিকরণ কারক পর্যন্ত। বাপ্ রে বাপ! মানুষে এত পড়েই বা কখন এবং মনে রাখেই বা কি করিয়া!
ইহার পার্শ্বে ‘লাল শালু-মণ্ডিত বংশখণ্ড-নির্মিত ক্রীড়া-গাণ্ডীব’-ধারী নরেশচন্দ্র একেবারে চ্যাপটাইয়া গিয়াছেন। আজ ছেলেবেলার একটা ঘটনা মনে পড়িতেছে। আমাদের অবৈতনিক নব-নাট্যসমাজের বড় অ্যাক্টর ছিলেন নরসিংহবাবু। রাম বল, রাবণ বল, হরিশ্চন্দ্র বল, তাঁহারই ছিল একচেটে। হঠাৎ আর একজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁর নাম রাম-নরসিংবাবু। আরও বড় অ্যাক্টর! যেমন দরাজ গলার হুঙ্কার, তেমনি হস্ত-পদ সঞ্চালনের অপ্রতিহত পরাক্রম। যেন মত্তহস্তী। এই নবাগত রাম-নরসিংবাবুর দাপটে আমাদের শুধু নরসিংবাবু একেবারে তৃতীয়ার শশিকলার ন্যায় পাণ্ডুর হইয়া গেলেন। নরেশবাবুকে দেখি নাই, কিন্তু কল্পনায় তাঁহার মুখের চেহারা দেখিয়া বোধ হইতেছে, যেন তিনি যুক্ত-হস্তে চতুরাননকে গিয়া বলিতেছেন, প্রভু! ইহার চেয়ে যে আমার বনে বাস করা ভাল!
দ্বিজেন্দ্রবাবুর তর্ক করিবার রীতিও যেমন জোরালো, দৃষ্টিও তেমনি ক্ষুরধার। রায়ের মুসাবিদায় কোথাও একটি অক্ষরও যেন ফাঁক না পড়ে এমনি সতর্কতা। যেন বেড়াজালে ঘেরিয়া রুই-কাতলা হইতে শামুক-গুগলি পর্যন্ত ছাঁকিয়া তুলিতে বদ্ধপরিকর।
হায় রে বিচার! হায় রে সাহিত্যের রস! মথিয়া মথিয়া আর তৃপ্তি নাই। ডাইনে ও বামে রবীন্দ্রনাথ ও নরেশচন্দ্রকে লইয়া অক্লান্তকর্মী দ্বিজেন্দ্রনাথ নিরপেক্ষ সমান-তালে যেন তুলাধুনা করিয়াছেন।
কিন্তু ততঃ কিম্?
এই কিম্টুকুই কিন্তু ঢের বেশী চিন্তার কথা। নরেশচন্দ্র অথবা দ্বিজেন্দ্রনাথ ইঁহারা সাহিত্যিক মানুষ। ইঁহাদের ভাব-বিনিময় ও প্রীতি-সম্ভাষণ বুঝা যায়। কিন্তু এই সকল আদর-আপ্যায়নের সূত্র ধরিয়া যখন বাহিরের লোকে আসিয়া উৎসবে যোগ দেয়, তখন তাহাদের তাণ্ডব-নৃত্য থামাইবে কে?
একটা উদাহরণ দিই। এই আশ্বিনের ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় শ্রীব্রজদুর্ল্লভ হাজরা বলিয়া এক ব্যক্তি রস ও রুচির আলোচনা করিয়াছেন। ইঁহার আক্রমণের লক্ষ্য হইতেছে তরুণের দল। এবং নিজের রুচির পরিচয় দিতে গিয়া বলিতেছেন, “এখন যেরূপ রাজনীতির চর্চায় শিশু ও তরুণ, ছাত্র ও বেকার ব্যক্তি সতত নিরত”, সেইরূপ অর্থোপার্জনের জন্যই এই বেকার সাহিত্যিকের দল গ্রন্থরচনায় নিযুক্ত। এবং তাহার ফল হইয়াছে এই য, “হাঁড়ি চড়াইয়া কলম ধরিলে যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে।”
এই ব্যক্তি ডেপুটিগিরি করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে এবং আজীবন গোলামির পুরস্কার মোটা পেনশনও ইহার ভাগ্যে জুটিয়াছে। তাই সাহিত্যসেবীর নিরতিশয় দারিদ্র্যের প্রতি উপহাস করিতে ইহার সঙ্কোচের বাধা নাই। লোকটি জানেও না যে, দারিদ্র্য অপরাধ নয়, এবং সর্বদেশে ও সর্বকালে ইহারা অনশনে প্রাণ দিয়াছে বলিয়াই সাহিত্যের আজ এত বড় গৌরব।
ব্রজদুর্ল্লভবাবু না জানিতে পারেন, কিন্তু ‘প্রবাসী’র প্রবীণ ও সহৃদয় সম্পাদকের ত এ কথা অজানা নয় যে, সাহিত্যের ভালো-মন্দর আলোচনা ও দরিদ্র সাহিত্যিকের হাঁড়ি-চড়া না-চড়ার আলোচনা ঠিক এক বস্তু নয়। আমার বিশ্বাস, তাঁহার অজ্ঞাতসারেই এতবড় কটূক্তি তাঁহার কাগজে ছাপা হইয়া গেছে, এবং এজন্য তিনি ব্যথাই অনুভব করিবেন, এবং হয়ত, তাঁহার লেখকটিকে ডাকিয়া কানে কানে বলিয়া দিবেন, বাপু, মানুষের দৈন্যকে খোঁটা দেওয়ার মধ্যে যে রুচি প্রকাশ পায় সেটা ভদ্রসমাজের নয়, এবং ঘটি-চুরির বিচারে পরিপক্কতা অর্জন করিলেই সাহিত্যের ‘রসে’র বিচারে অধিকার জন্মায় না। এ দুটোর প্রভেদ আছে,—কিন্তু সে তুমি বুঝিবে না।—ইতি ৫ই আশ্বিন, ১৩৩৪। (‘আত্মশক্তি, ১৩ই আশ্বিন ১৩৩৪)
রসচক্র
রাজশাহী শহরের ক্রোশ-কয়েক দূরে বিরাজপুর গ্রাম। গ্রামটি বড়,—বহু ঘর ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থের বাস। কিন্তু মৈত্র-বংশের সততা, সাধুতা এবং স্বধর্মর্নিষ্ঠার খ্যাতি গ্রাম উপচাইয়া শহর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহাদের বিষয়-সম্পত্তি যাহা ছিল, তাহাতে মোটা ভাত-কাপড়টাই কোনমতে চলিতে পারিত, কিন্তু তাহার অধিক নয়। অথচ ক্রিয়াকলাপ কোনটাই বাদ পড়িবার জো ছিল না। অনেকখানি স্থান ব্যাপিয়া ভদ্রাসন, অনেকগুলি মেটে খোড়ো ঘর, মস্তবড় চণ্ডীমণ্ডপ;—ইহার সকলগুলিই সকল সময়েই পরিপূর্ণ।
কিন্তু এ-সব হইত কি করিয়া? হইত, উপস্থিত তিন ভাই-ই উপার্জন করিতেন বলিয়া। বড়, শিবরতন গ্রামেই জমিদারি-রাজসরকারে ভাল চাকরি করিতেন; সেজ, শম্ভুরতন শেয়ারের গাড়িতে জেলা আদালতে পেশকারি করিতে যাইতেন, কেবল ন’ বিভূতিরতন, ধনী শ্বশুরের কৃপায় কলিকাতায় থাকিয়া কোন একটা বড় সওদাগরী অফিসে বড় কাজ পাইয়াছিলেন। মেজ এবং ছোটভাই শিশুকালেই মারা পড়িয়াছিল, তালিকায় ওই দুটা শূন্যস্থান ব্যতীত আর তাহাদের কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।
দিন-দুই হইল দুর্গাপূজা শেষ হইয়া গেছে; প্রতিমার কাঠামোটা উঠানের একধারে আড়াল করিয়া রাখা হইয়াছে,—সহসা চোখ না পড়ে; কেবল তাঁহার মঙ্গলঘটটি আজিও বেদীর পার্শ্বে তেমনি বসানো আছে। তাহার আম্রপল্লব আজিও তেমনি স্নিগ্ধ, তেমনি সজীব রহিয়াছে,—এখনও একবিন্দু মলিনতা কোথাও স্পর্শ করে নাই।
সকালে ইহারই অদূরে একটা বড় সতরঞ্চির উপর বসিয়া তিন ভাইয়ের মধ্যে বোধ হয় খরচপত্রের আলোচনাটাই এইমাত্র শেষ হইয়া একটু বিরাম পড়িয়াছিল, বিভূতিরতন একটু ইতস্ততঃ করিয়া একটু সঙ্কোচের সহিত মুখখানা হাসির মত করিয়া কহিল, সেদিন শাশুড়ী-ঠাকরুন আশ্চর্য হয়ে বলছিলেন, তোমার মাইনের সমস্ত টাকাটা একদফা বাড়িতে দাদার কাছে পাঠিয়ে দিতে হয়। তিনি আবার দরকারমত কিছু নিয়ে বাকিটা ফিরে পাঠিয়ে দেন, এতে মাসে মাসে অনেকগুলো টাকা পোস্টাফিসকে দিতে হয়।
সংসার-খরচের খাতাখানা তখনও শিবরতনের সম্মুখে খোলা ছিল,—এবং চক্ষুও তাঁহার তাহাতেই আবদ্ধ ছিল, অনেকটা অন্যমনস্কের মত বলিলেন, পোস্টাফিস মনি-অর্ডারের টাকা ছাড়বে কেন হে? এতে আশ্চর্য হবার কি আছে?
বিভূতির ধনী শ্বশ্রূঠাকুরানীর যে কিছুদিন হইতেই কন্যা-জামাতার সাংসারিক উন্নতির প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে, এ সংশয় শিবরতনের জন্মিয়াছিল। কিন্তু কণ্ঠস্বরে কিছুই প্রকাশ পাইল না।
বিভূতি মনে করিল, দাদা ঠিকমত কথাটাতে কান দেন নাই, তাই আরও একটু স্পষ্ট করিয়া কহিল, আজ্ঞে হাঁ, তা ত বটেই। তাই তিনি বলেন, আপনার আবশ্যকমত টাকাটাই যদি শুধু—
শিবরতন চোখ তুলিয়া চাহিলেন; বলিলেন, আমার আবশ্যক তোমরা জানবে কি করে?
তাঁহার মুখের উপর তেমনি সহজ ও শান্ত ভাব দেখিয়া বিভূতির সাহস বাড়িল, সে প্রফুল্ল হইয়া কহিল, আজ্ঞে হাঁ, তাই তিনি বলছিলেন, আপনার চিঠিপত্রের মধ্যে তার একটুখানি আভাস থাকলেও এই বাজে-খরচটা আর হতে পারত না। শিবরতন তাঁহার হিসাবের খাতার প্রতি পুনরায় দৃষ্টি আনত করিয়া জবাব দিলেন, তাঁকে বলো, দাদা একে বাজে-খরচ বলেও মনে করেন না, চিঠিপত্রে আভাস দেওয়াও দরকার ভাবেন না। যোগীন, তামাক দিয়ে যা।
বিভূতি পাংশু-মুখে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল এবং শম্ভু দাদার আনত মুখের প্রতি কটাক্ষে চাহিয়া হাতের খবরের কাগজে মনোনিবেশ করিল।
কিছুক্ষণ পর্যন্ত কাহারো মুখেই কথা রহিল না,—একটা অবাঞ্ছিত নীরবতায় ঘর ভরিয়া রহিল। কিন্তু ইহার অর্থ বুঝিতে হইলে এই মৈত্র-বংশের ইতিবৃত্তটাকে আরও একটু পরিস্ফুট করা প্রয়োজন।
এই বিরাজপুরে ইঁহাদের সাত-আট পুরুষেরও অধিককাল বাস হইয়া গেছে, অনেক ঘর-দ্বার ভাঙ্গাগড়া হইয়াছে, অনেক ঘর-দ্বার আবশ্যকমত বাড়ানো-কমানো হইয়াছে। কিন্তু সাবেক-দিনের সেই রন্ধনশালাটি আজও তেমনি একমাত্র ও অদ্বিতীয় হইয়াই রহিয়াছে। কখনো তাহাকে বিভক্ত করা হয় নাই, কখনো তাহাতে আর একটা সংযুক্ত করিবার কল্পনা পর্যন্ত হয় নাই। এই পরিবার চিরদিন একান্নবর্তী, চিরদিনই যিনি বড়, তিনি বড় থাকিয়াই জীবনপাত করিয়া গেছেন—পরে জন্মিয়া অগ্রজের সর্বময় কর্তৃত্বকে কেহ কোনদিন প্রশ্ন করিবার অবকাশ পর্যন্ত পায় নাই।
সেই বংশের আজ যিনি বড়, সেই শিবরতন যখন ছোটভাইয়ের অত্যন্ত দুরূহ সমস্যার শুধু কেবল একটা ‘প্রয়োজন নাই’ বলিয়াই নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন, তখন বড়মানুষ শ্বশুর-শাশুড়ীর নিরতিশয় ক্রুদ্ধ মুখ মনে করিয়াও বিভূতির এমন সাহস হইল না যে, এই বিতর্কের একটুকুও জের টানিয়া চলে।
চাকর তামাক দিয়া গেল, শিবরতন খাতা বন্ধ করিয়া তাহা হাতবাক্সে বন্ধ করিয়া অত্যন্ত ধীরেসুস্থে ধূমপান করিতে করিতে বলিলেন, তোমার ছুটি আর ক’দিন রইল বিভূতি?
আজ্ঞে ছ’দিন।
শিবরতন মনে মনে হিসাব করিয়া বলিলেন, তা হলে শুক্রবারেই তোমাকে রওনা হতে হবে দেখছি।
বিভূতি মৃদুকণ্ঠে বলিল, আজ্ঞে হাঁ। কিন্তু এই সময়টায় বড় বেশী কাজকর্ম, তাই—
শিবরতন কহিলেন, তা বেশ। না হয়, দু’দিন পূর্বেই যাও। দেবীপক্ষ—দিনক্ষণ দেখার আর আবশ্যক নেই,—সবই সুদিন। তা হলে পরশু বুধবারেই রওনা হয়ে পড়, কি বল?
বিভূতি কহিল, যে আজ্ঞে, তাই যাবো।
শিবরতন আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ধূমপান করিয়া একটু হাসিয়া কহিলেন, ন-বৌমার কাছে বড় অপ্রতিভ হয়ে আছি। গত বৎসর তাঁকে একপ্রকার কথাই দিয়েছিলাম যে, এ বৎসর তাঁর ছুটি,—এ বৎসর বাপের বাড়িতে তিনি পূজো দেখবেন। কিন্তু দিন যত ঘনিয়ে আসতে লাগল ততই ভয় হতে লাগল, তিনি না থাকলে ক্রিয়াকর্ম যেন সমস্ত বিশৃঙ্খল, সমস্ত পণ্ড হয়ে যাবে। আদর-অভ্যর্থনা করতে, সকল দিকে দৃষ্টি রাখতে তাঁর ত আর জোড়া নেই কিনা! এত কাজ, এত গণ্ডগোল, এত হাঙ্গামা, কিন্তু কখনো মাকে বলতে শুনলাম না—এটা দেখিনি, কিংবা এটা ভুলে গেছি। অন্য সময়ে সংসার চলে,—বড়বৌ ও সেজবৌমাই দেখতে পারেন, কিন্তু বৃহৎ কাজকর্মের মধ্যে আমার ন-বৌমা নেই মনে করলেই ভয়ে যেন আমার হাত-পা গুটিয়ে আসে,—কিছুতে সাহস পাইনে। এই বলিয়া স্নেহে, শ্রদ্ধায় মুখখানি দীপ্ত করিয়া তিনি পুনরায় নীরবে ধূমপান করিতে লাগিলেন।
বড়কর্তার ন-বৌমার প্রতি বিশেষ একটু পক্ষপাতিত্ব আছে, ইহা লইয়া বাটীর মধ্যে আলোচনা ত হইতই, এমন কি একটা ঈর্ষার ভাবও ছিল। বড়বধূ রাগ করিয়া মাঝে মাঝে ত স্পষ্ট করিয়াই স্বামীকে শুনাইয়া দিতেন; এবং সেজবধূ আড়ালে অসাক্ষাতে এরূপ কথাও প্রচার করিতে বিরত হইতেন না যে, ন-বৌ শুধু বড়লোকের মেয়ে বলিয়াই এই খোশামোদ করা। নইলে আমরা দু-জায়ে এগারো মাসই যদি গৃহস্থালীর ভার টানতে পারি ত পূজোর মাসটা আর পারি না! বড়মানুষের মেয়ে না এলেই কি মায়ের পূজো আটকে যাবে?
এই-সকল প্রচ্ছন্ন শব্দভেদী বাণ যথাকালে যথাস্থানে আসিয়াই পৌঁছিত, কিন্তু শিবরতন না হইতেন বিচলিত, না করিতেন প্রতিবাদ। হয়ত বা কেবল একটুখানি মুচকিয়া হাসিতেন মাত্র। বিভূতি অধিক উপার্জন করে, তাহাকে বারোমাস বাসা করিয়া কলিকাতাতেই থাকিতে হয়, সুতরাং ন-বধূমাতার তথায় না থাকিলে নয়। এ কথা তিনি বেশ বুঝিতেন, কিন্তু অবুঝের দল কোনমতেই স্বীকার করিতে চাহিত না। তাহাদের একজনকে সংসারে মামুলি এবং মোটা কাজগুলা সারা বৎসর ধরিয়াই করিতে হয় না। কেবল মহামায়ার পূজা উপলক্ষে হঠাৎ একসময়ে আসিয়া সমস্ত দায়িত্ব, সকল কর্তৃত্ব, নিজের হাতে লইয়া তাহা নির্বিঘ্নে শেষ করিয়া দিয়া, ঘরের এবং পরের সমস্ত সুখ্যাতি আহরণ করিয়া লইয়া চলিয়া যায়,—সে না থাকিলে এ-সব যেন কিছু হইতে পারিত না, সমস্তই যেন এলোমেলো হইয়া উঠিত, লোকের মুখের ও চোখের এই-সকল ইঙ্গিতে মেয়েদের চিত্ত একেবারে দগ্ধ হইয়া যাইত। কাজকর্ম অন্তে এই লইয়া প্রতি বৎসরেই কিছু-না-কিছু কলহ-বিবাদ হইতই। বিশেষ করিয়া মা আজও জীবিত আছেন এবং আজও তিনিই গৃহিণী। কিন্তু বয়স অত্যন্ত বেশী হইয়া পড়ায় অপরের দোষ-ত্রুটি দেখাইয়া তিরস্কার ও গালি-গালাজ করার কাজটুকু মাত্র হাতে রাখিয়া গৃহিণীপনার বাকি সমস্ত দায়িত্বই তিনি স্বেচ্ছায় বড় ও সেজ-বধূমাতার হাতে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। তিনি ন-বৌকে একেবারে দেখিতে পারিতেন না। সে সুন্দরী, সে বড়লোকের মেয়ে, তাহার কাপড়-গহনা প্রয়োজনের অতিরিক্ত, তাহাকে সংসার করিতে হয় না, সে চিঠি লিখিতে পারে, অহঙ্কারে তাহার মাটিতে পা পড়ে না, ইত্যাদি নালিশ এগারো মাস-কাল নিয়ত শুনিতে শুনিতে এই বধূটির বিরুদ্ধে মন তাঁহার তিক্ততায় পরিপূর্ণ হইয়া থাকিত; এবং এই দীর্ঘকাল পরে সে যখন গৃহে প্রবেশ করিত, তখন তাহা অনধিকার-প্রবেশের মতই তাঁহার ঠেকিত।
কাল হইতে একটা কথা উঠিয়াছে যে, ধরণী সাণ্ডেলদের বাড়ির মেয়েদের সরায় সন্দেশ দুটো করিয়া কম পড়িয়াছিল এবং কম পড়িয়াছিল কেবল তাহারা গরীব বলিয়াই। এই দুর্নাম শুধু গ্রামে নয়, তাহা শহর ছাড়াইয়া নাকি বিলাত পর্যন্ত পৌঁছিবার উপক্রম করিয়াছে,—এই দুঃসংবাদ গৃহিণীর কানে গেল যখন তিনি আহ্নিকে বসিতেছিলেন।
তখন হইতে ছত্রিশ ঘণ্টা কাটিয়া গেছে,—মালা-আহ্নিকের যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটিয়াছে, কিন্তু আলোচনার শেষ হইতে পায় নাই। দোষ শুধু ন-বৌমার এ বিষয়েও যেমন কাহারও সংশয় ছিল না, এবং নিজে সে বড়লোকের মেয়ে বলিয়াই ইচ্ছা করিয়া দরিদ্র পরিবারের অপমান করিয়াছে, ইহাতেও তেমনি কাহারও সন্দেহ ছিল না। ন-বৌ যে সকল কথাই নীরবে সহ্য করিয়া যাইত তাহা নয়,—মাঝে মাঝে সেও উত্তর দিত; কিন্তু তাহার কোন উত্তরটাই সোজা শাশুড়ির কানে পৌঁছিত না, পৌঁছিত প্রতিধ্বনিত হইয়া। তাই তাহার বক্তব্যটা লোকের মুখে মুখে ঘা খাইয়া কেবল বিকৃতই হইত না, তাহার রেশটাও সহজে মিলাইতে চাইত না। সকালে আজ বাটীর মধ্যে যখন এই অবস্থা,—সান্যাল-পরিবারের মিষ্টান্নের ন্যূনতা লইয়া ন-বধূর সম্বন্ধে আলোচনা যখন তুমুল হইয়া উঠিয়াছে, বাহিরে তখন শিবরতন সেই ন-বধূমাতারই প্রশংসায় মুক্তকণ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন।
শিবরতন কহিলেন, বুধবারে ন-বৌমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাও। মা আমার আরও কিছুদিন এখানে থেকে যেতে পারলে যেখানে যা-সমস্ত গুছিয়ে-গাছিয়ে সারা বছরের জন্যে আমাকে নিশ্চিন্ত করে যেতে পারতেন, কেননা, এ-সকল কাজ আর কোন বৌয়ের দ্বারাই অমন শৃঙ্খলায় হয় না,—কিন্তু কি আর করা যাবে! নিয়ে গিয়ে দু-দশদিন তাঁর মায়ের কাছে দিয়ো, তবু বোনদের সঙ্গে দিন-কতক আনন্দে কাটাতে পারবেন। বিভূতি, তোমার বাসায় ত বিশেষ কোন অসুবিধা হবে না?
বিভূতি কহিল, আজ্ঞে না, অসুবিধা কিছুই হবে না।
শিবরতন বলিলেন, বেশ তাই করো। ন-বৌমা বাড়ি ছেড়ে যাবেন মনে হলেও আমার বিজয়ার দুঃখ যেন বেশী করে উথলে ওঠে,—কিন্তু কি আর করা যাবে! সবই মহামায়ার ইচ্ছা। সারা বছর সবাইকে নিয়ে সংসার করা—বলিয়া তিনি একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস চাপিয়া ফেলিয়া বোধ করি আরও কি একটু বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ উপস্থিত সকলেই একেবারে চমকিত হইয়া উঠিলেন।
বৃদ্ধা জননী কাঁদিতে কাঁদিতে একেবারে প্রাঙ্গণের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। শিবরতন শশব্যস্তে হুঁকা রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, শম্ভু এবং বিভূতি তাহারাও অগ্রজের সঙ্গে দাঁড়াইয়া উঠিল, মা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—শিবু, আমার গুরু দিব্যি রইল, তোদের বাড়িতে আর আমি জলগ্রহণ করব না, যদি না এর বিচার করিস। ন-বৌ বড়লোকের বেটী, আজ আমাকে জুতো ছুঁড়ে মেরেছে!
সম্মুখে বজ্রাঘাত হইলেও বোধ করি ভাইয়েরা অধিক চমকিত হইতেন না। বিভূতি ভয়ে পাংশু হইয়া উঠিল, শিবরতন বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া বলিয়া উঠিলেন, ন-বৌমা! একি কখনো হতে পারে মা?
মা তেমনি রোদন-বিকৃতকণ্ঠে কহিলেন, হয়েও কাজ নেই বাবা, ও যে ন-বৌ !
বড়লোকের মেয়ে ! তা যাই হোক, যখন গুরুর নাম নিয়ে দিব্যি করেচি, তখন বাড়িতে রেখে বুড়ো মাকে আর মেরো না বাবা, আজই কাশী পাঠিয়ে দাও। যাই তাঁদের চরণেই আশ্রয় নিই গে।
দেখিতে দেখিতে ছেলেমেয়ে দাসী-চাকরে প্রায় ভিড় হইয়া উঠিয়াছিল, শিবরতন তাঁর ছোটমেয়ে গিরিবালার প্রতি চাহিয়া কহিলেন, কি হয়েচে রে, গিরি, তুই জানিস?
গিরিবালা মাথা নাড়িয়া বলিল, জানি বাবা!—এই বলিয়া সে সাণ্ডেলদের সরায় সন্দেশ কম হইবার বিবরণ সবিস্তারে বিবৃত করিয়া কহিল, ঠাকুরমা ন-খুড়ীমাকে বড্ড গালাগালি দিচ্ছিলেন, বাবা।
শিবরতন কহিলেন, তার পর?
মেয়ে বলিল, ন-খুড়ীমা মুখ বুজে ঝাঁট দিচ্ছিলেন, সুমুখে ন-কাকার জুতোজোড়াটা ছিল, তাই পা দিয়ে শুধু ফেলে দিয়েছিলেন।
শিবরতন প্রশ্ন করিলেন, তার পরে?
গিরি কহিল, এক পাটি জুতো ছিটকে এসে ঠাকুরমার পায়ের কাছে পড়েছিল।
শিবরতন শুধু কহিলেন, হুঁ! মায়ের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, ভেতরে যাও মা! এর বিচার যদি না হয়, ত তখন কাশীতেই চলে যেয়ো।
একে একে ধীরে ধীরে সবাই প্রস্থান করিল, শুধু কেবল তিন ভাই সেইখানে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। ভৃত্য তামাক দিয়া গেল, কিন্তু সে শুধু পুড়িতেই লাগিল, শিবরতন স্পর্শ করিলেন না, প্রায় আধ-ঘণ্টাকাল এইভাবে নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া অবশেষে মুখ তুলিয়া বলিলেন, বিভূতি?
বিভূতি সসম্ভ্রমে কহিল, আজ্ঞে?
শিবরতন বলিলেন, তোমার স্ত্রীর শাস্তি তুমি ছাড়া আর কারও দেবার অধিকার নেই।
বিভূতি আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া ক্ষীণকণ্ঠে বলিল, আজ্ঞা করুন।
শিবরতন বলিলেন, ঐ জুতো তোমার স্ত্রীর মাথায় তুমি তুলে দেবে। উঠানের মাঝখানে তিনি মাথায় নিয়ে সমস্ত বেলা দাঁড়িয়ে থাকবেন। তোমার উপর এই আমার আদেশ।
আদেশ শুনিয়া বিভূতির মাথার মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ বহিয়া গেল। তাহার শ্বশুর-শাশুড়ীর মুখ, শালী-শালাদের মুখ, চাকরির মুখ, স্ত্রীর মুখ, সমস্ত একই সঙ্গে মনে পড়িয়া মুখখানা ভয়ে ভাবনায় বিবর্ণ হইয়া উঠিল, সে জড়িত-কণ্ঠে কহিতে চাহিল,—কিন্তু দাদা, দোষের বিচার না করেই—
শিবরতন শান্তস্বরে কহিলেন, মা অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছেন, এ তোমরাও দেখলে। তাঁর কি দোষ, কতখানি দোষ, এ বিচারের ভার আমার ওপর নেই। যাঁদের বিচার করতে পারি তাঁদের প্রতি আমার এই আদেশ রইল। এখন কি করবে সে তুমি জানো।
বিভূতি কহিল, আপনার হুকুম চিরদিন মাথায় বয়ে এসেছি দাদা, কোনদিন কোন স্বাধীনতা পাইনি। আজও তাই হবে, কিন্তু—
এই কিন্তুটা সেও শেষ করিতে পারিল না, শিবরতনও নীরবে অধোমুখে বসিয়া রহিলেন।
বিভূতি ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বোধ করি বা দাদার কাছে কিছু প্রত্যাশা করিল। কিন্তু কিছুই না পাইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, দাদা, আমি চললুম—এই বলিয়া সে ধীরে ধীরে
অন্তঃপুরের অভিমুখে প্রস্থান করিল।
শিবরতন কোন কথা কহিলেন না, তেমনি অধোমুখে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। পূজার বাড়ি, আজও আত্মীয়, অনাত্মীয়, কুটুম্ব, প্রতিবেশী ছেলেমেয়ে চাকর-দাসীতে পরিপূর্ণ। এই-সকলের মাঝখানে যে ন-বউমা তাঁহার প্রাণাধিক স্নেহের পাত্রী, তাঁহারই এতবড় অপমান, এতবড় শাস্তি যে কি করিয়া অনুষ্ঠিত হইবে, তাহা তিনি নিজেও ভাবিয়া পাইলেন না। তাঁহার নতনেত্র হইতে বড় বড় তপ্ত অশ্রুর ফোঁটা টপটপ করিয়া মেঝের উপর ঝরিয়া পড়িতে লাগিল,—কিন্তু ‘বিভূতি’ বলিয়া একবার ফিরিয়া ডাকিতে পারিলেন না। কেবল মনে মনে প্রাণপণ বলে বলিতে লাগিলেন—কিন্তু, কিন্তু মা যে! মা যে! তাঁর যে অপমান হয়েছে!
শুভেচ্ছা
শারদীয়া পূজা বাঙ্গালীর সবচেয়ে বড় উৎসব। এর প্রতি বাঙ্গালীর নরনারীর ঔৎসুক্যেরও অবধি নাই, স্নেহেরও অন্ত নাই। তাই এ প্রকাশ পায় তাদের আনন্দের নানা পথে, নানা বিচিত্র গতিতে। কোথাও বা অন্তর্মুখী—মানুষের আপন গৃহে ফিরে আসার তাড়া, আত্মীয়-স্বজনগণের সামীপ্য কামনা। আর কোথাও বা বহির্মুখী—ঘর ছেড়ে বাহিরে যাবার তাগিদ।
যে অপরিচিত আজও অজানা, তাঁদের আপন করে জানার ব্যাকুলতা। সুতরাং, সেদিন যখন শিলং পাহাড়ের হেমচন্দ্র এসে বললেন, এবার পূজায় তাঁরা একখানি কাগজ বার করবেন, আমি বিস্মিত হইনি, এ ভালোই হল যে, এঁদের আনন্দোৎসবের ধারা এবার সাহিত্যসেবার খাতে প্রবাহিত হবে। এ আয়োজন সম্পূর্ণ ও সুন্দর করবার শ্রম আছে, ব্যয় আছে,—সে থাক—তবু, সমস্তকে অতিক্রম করেও একাগ্র সাধনার যে সফলতা বাণীর প্রসাদস্বরূপ এঁরা পাবেন, তাতে অকলঙ্ক আনন্দরস মধুরতর দীপ্ততর হয়ে উঠবে।
কিন্তু একটা কথা বলারও আছে। আমি জানি, আমার এই কয়ছত্র মাত্র লেখার মূল্য কিছু নেই, থাকা সম্ভবও নয়। কারণ, শক্তি যাদের নিঃশেষিতপ্রায়, আয়ুঃ অস্তোন্মুখ, তাঁদের কাছে প্রত্যাশা করা আর চলে না। তবু এই আগন্তুক পত্রিকাখানির ক্ষতি হবে না। সাহিত্যব্রতে যাঁরা নবীন পথিক, যাঁরা উদীয়মান, বেগ যাঁদের চঞ্চল গতিশীল, এই বাণীপূজার মহৎ অর্ঘ্য তাঁদের কাছ থেকেই সম্পূর্ণ সমাহৃত হবে, এই আমার আশা। শিলং–এর বাঙ্গালী অধিবাসীগণের পক্ষে হেম চেয়েছিলেন শুধু আমার কাছে আশীর্বাদ; তাঁদের শারদবার্ষিকীর জন্য শুভ কামনা। একান্ত মনে প্রার্থনা করি, তাঁদের যত্ন, তাঁদের সাধনা সার্থক হোক, এই বাৎসরিক সাহিত্য পত্রিকাখানির আয়ু যেন সুদীর্ঘ হয়। এ যেন এমনি করেই বর্ষে বর্ষে ফিরে আসে। ইতি — ১৪ই ভাদ্র, ১৩৪১।
(১৩৪১ সালের ‘শিলং বার্ষিক পত্রিকা’)
সত্য ও মিথ্যা
এক
পিতলকে সোনা বলিয়া চালাইলে সোনার গৌরব ত বাড়েই না, পিতলটারও জাত যায়। অথচ সংসারে ইহার অসদ্ভাব নাই। জায়গা ও সময়-বিশেষে হ্যাট মাথায় দিয়া খাতির আদায় করা যাইতে পারে, কিন্তু চোখ বুজিয়া একটুখানি দেখিবার চেষ্টা করিলেই দেখা অসম্ভব নয় যে, একদিকে এই খাতিরটাও যেমন ফাঁকি, মানুষটার লাঞ্ছনাও তেমনি বেশী। তবুও এ চেষ্টার বিরাম নাই। এই যে সত্য গোপনের প্রয়াস, এই যে মিথ্যাকে জয়যুক্ত করিয়া দেখানো, এ কেবল তখনই প্রয়োজন হয়, মানুষ যখন নিজের দৈন্য জানে। নিজের অভাবে লজ্জা বোধ করে, কিন্তু এমন বস্তু কামনা করে, যাহাতে তাহার যথার্থ দাবী-দাওয়া নাই।এই অসত্য অধিকার যতই বিস্তৃত ও ব্যাপক হইয়া পড়িতে থাকে, অকল্যাণের স্তূপও ততই প্রগাঢ় ও পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতে থাকে। আজ এই দুর্ভাগা রাজ্যে সত্য বলিবার জো নাই, সত্য লিখিবার পথ নাই—তাহা সিডিশন। অথচ দেখিতে পাই, বড়লাট হইতে শুরু করিয়া কনস্টেবল পর্যন্ত সবাই বলিতেছেন—সত্যকে তাঁহারা বাধা দেন না, ন্যায়সঙ্গত সমালোচনা—এমন কি, তীব্র ও কটু হইলেও নিষেধ করেন না। তবে বক্তৃতা বা লেখা এমন হওয়া চাই, যাহাতে গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে লোকের ক্ষোভ না জন্মায়, ক্রোধের উদয় না হয়। চিত্তের কোনপ্রকার চাঞ্চল্যের লক্ষণ না দেখা দেয়,—এমনি। অর্থাৎ, অত্যাচার-অবিচারের কাহিনী এমন করিয়া বলা চাই, যাহাতে প্রজাপুঞ্জের চিত্ত আনন্দে আপ্লুত হইয়া উঠে, অন্যায়ের বর্ণনায় প্রেমে বিগলিত হইয়া পড়ে এবং দেশের দুঃখ-দৈন্যের ঘটনা পড়িয়া দেহ-মন যেন তাহাদের একেবারে স্নিগ্ধ হইয়া যায়! ঠিক এমনটি না ঘটিলেই তাহা রাজ-বিদ্রোহ। কিন্তু এ অসম্ভব কি করিয়া সম্ভব করি? দুইজন পাকা ও অত্যন্ত হুঁশিয়ার এডিটারকে একদিন প্রশ্ন করিলাম। একজন মাথা নাড়িয়া জবাব দিলেন,—ওটা ভাগ্য। অদৃষ্ট প্রসন্ন থাকিলে সিডিশন হয় না—ওটা বিগড়াইলেই হয়! আর একজন পরামর্শ দিলেন,—একটা মজা আছে। লেখার গোড়ায় ‘যদি’ এবং শেষে ‘কিনা’? দিতে হয় এবং এই দুটো কথা নির্বিচারে সর্বত্র ছড়াইয়া দিতে পারিলে আর সিডিশনের ভয় থাকে না। হবেও বা, বলিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া আসিলাম—কিন্তু আমার পক্ষে একের পরামর্শও যেমন দুর্বোধ, অপরের উপদেশও তেমনি অন্ধকার ঠেকিল।
লিখিয়া লিখিয়া নিজেও বুড়া হইলাম,নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিবেক-মতই কোন একটা বিষয় ন্যায়সঙ্গত কিনা স্থির করিতে পারি, কিন্তু যাহার আলোচনা করিতেছি, তাহার রুচি ও বিবেচনার সহিত কাঁধ মিলাইবার দুঃসাধ্য চেষ্টায় কি করিয়া যে লেখার আগাগোড়ায় ‘যদি’ ও ‘কিনা’ বিকীর্ণ করিয়া সিডিশন বাঁচাইব, ইহাও যেমন আমার বুদ্ধির অতীত, জ্যোতিষীর কাছে নিজের ভাগ্য যাচাইয়া তবে লেখা আরম্ভ করিব, সেও তেমনি সাধ্যের অতিরিক্ত। অতএব সত্য ও মিথ্যা নির্ণয়ের চেষ্টায়, ইহার কোনটাই আমি সম্প্রতি পারিয়া উঠিব না। তবে প্রয়োজন হইলে নিজের দুর্ভাগ্যকে অস্বীকার করিব না।
এই প্রবন্ধটা বোধ করি কিছু দীর্ঘ হইয়া পড়িবে, সুতরাং ভূমিকায় এই কথাটাই আরও একটু বিশদ করিয়া বলা প্রয়োজন। একদিন এ দেশ সত্যবাদিতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, কিন্তু আজ ইহার দুর্দশার অন্ত নাই। সত্য-বাক্য সমাজের বিরুদ্ধে বলা যেমন কঠিন, রাজশক্তির বিরুদ্ধে বলা ততোধিক কঠিন। সত্য লেখা যদি-বা কেহ লেখে, ছাপাওয়ালারা ছাপিতে চায় না,—প্রেস তাহাদের বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। লেখা যাঁহাদের পেশা, জীবিকার জন্য দেশের সংবাদপত্রের সম্পাদকতা যাঁহাদের করিতে হয়, অসংখ্য আইনের শতকোটি নাগপাশ বাঁচাইয়া কি দুঃখেই না তাঁহাদের পা ফেলিতে হয়। মনে হয়, প্রত্যেক কথাটি যেন তাঁহারা শিহরিতে শিহরিতে লিখিয়াছেন। মনে হয়, রাজরোষে প্রত্যেক ছত্রটির উপর দিয়া যেন তাঁহাদের ক্ষুব্ধ ব্যথিত চিত্ত কলমটার সঙ্গে নিরন্তর লড়াই করিতে করিতেই অগ্রসর হইয়াছে। তবুও সেই অতি সতর্কভাষার ফাঁকে ফাঁকে যদি কদাচিৎ সত্যের চেহারা চোখে পড়ে, তখন তাহার বিক্ষত, বিকৃত মূর্তি দেখিয়া দর্শকের চোখ দুটাও যেন জলে ভরিয়া আসে। ভাষা যেখানে দুর্বল, শঙ্কিত, সত্য যে দেশে মুখোশ না পরিয়া মুখ বাড়াইতে পারে না, যে রাজ্যে লেখকের দল এতবড় উঞ্ছবৃত্তি করিতে বাধ্য হয়, সে দেশে রাজনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি সমস্তই যদি হাত ধরাধরি করিয়া কেবল নীচের দিকেই নামিতে থাকে, তাহাতে আশ্চর্য হইবার কি আছে? যে ছেলে অবস্থার বশে ইস্কুলে কাগজ-পেন্সিল চুরি করিবার ফন্দি শিখিতে বাধ্য হয়, আর একদিন বড় হইয়া সে যদি প্রাণের দায়ে সিঁদ কাটিতে শুরু করে, তখন তাহাকে আইনের ফাঁদে ফেলিয়া জেলে দেওয়া যায়। কিন্তু যে আইন প্রয়োগ করে, তাহার মহত্ত্ব বাড়ে না, এবং ইহার নিষ্ঠুর ক্ষুদ্রতায় দর্শকরূপে লোকের মনের মধ্যেও যেন সূঁচ বিঁধিতে থাকে।
দুই-একটা দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা বোধ করি আর একটু পরিস্ফুট হইবে। (‘বাঙলার কথা,’ ৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯২২)
দুই
সর্বদেশে সর্বকালে থিয়েটার জিনিসটা কেবল আনন্দ নয়, লোক-শিক্ষারও সাহায্য করে। বঙ্কিমবাবুর চন্দ্রশেখর বইখানা একসময়ে বাঙ্গালার স্টেজে প্লে হইত। লরেন্স ফস্টর বলিয়া এক ব্যক্তি ইংরাজ নীলকর অতিশয় কদাচারী বলিয়া ইহাতে লেখা আছে। কর্তাদের হঠাৎ একদিন চোখে পড়িল, ইহাতে ক্লাস হেট্রেড নাকি এমনি একটা ভয়ানক বস্তু আছে, যাহাতে অরাজকতা ঘটিতে পারে। অতএব অবিলম্বে বইখানা স্টেজে বন্ধ হইয়া গেল। থিয়েটারওয়ালারা দেখিলেন, ঘোর বিপদ। তাঁহারা কর্তাদের দ্বারে গিয়া ধন্না দিয়া পড়িলেন, কহিলেন—হুজুর, কি অপরাধ? কর্তারা বলিলেন, লরেন্স ফস্টর নামটা কিছুতেই চলিবে না, ওটা ইংরাজী নাম। অতএব ওটা ক্লাস হেট্রেড। থিয়েটারের ম্যানেজার কহিলেন, যে আজ্ঞা প্রভু! ইংরাজীনামটা বদলাইয়া এখানে একটা পর্তুগীজ নাম করিয়া দিতেছি। এই বলিয়া তিনি ডিক্রুজ, না ডিসিল্ভা, না কি এমনি একটা—যা মনে আসিল, অদ্ভুত শব্দ বসাইয়া দিয়া কহিলেন, এই নিন।
কর্তা দেখিয়া শুনিয়া কহিলেন, আর এই ‘জন্মভূমি’ কথাটা কাটিয়া দাও,—ওটা সিডিশন।
ম্যানেজার অবাক হইয়া বলিলেন, সে কি হুজুর, এদেশে যে জন্মিয়াছি!
কর্তা রাগিয়া বলিলেন, তুমি জন্মাইতে পার, কিন্তু আমি জন্মাই নাই। ও চলিবে না।
‘তথাস্তু’ বলিয়া ম্যানেজার শব্দটা বদলাইয়া দিয়া প্লে পাস করিয়া লইয়া ঘরে ফিরিলেন। অভিনয় শুরু হইয়া গেল। ক্লাস হেট্রেড হইতে আরম্ভ করিয়া মায় সিডিশন পর্যন্ত বিদেশী রাজশক্তির যত-কিছু ভয় ছিল, দূর হইল, ম্যানেজার আবার পয়সা পাইতে লাগিলেন। যাহারা পয়সা খরচ করিয়া তামাশা দেখিতে আসিল, তাহারা তামাশার অতিরিক্ত আরও যৎকিঞ্চিৎ সংগ্রহ করিয়া ঘরে ফিরিল—বাহির হইতে কোথাও কোন ত্রুটি লক্ষিত হইল না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সমস্ত বস্তুটা ছলনায় ও অসত্যের কালিতে কালো হইয়া রহিল। লরেন্স ফস্টর বলিয়া হয়ত কেহ ছিল না, ম্যানেজারের কল্পিত অদ্ভুত পর্তুগীজ নামটিও মিথ্যা। ব্যাপারটাও তুচ্ছ, কিন্তু ইহার ফল কোনমতেই তুচ্ছ নয়।
স্বর্গীয় গ্রন্থাকারের বোধ করি ইচ্ছা ছিল, সে-সময়ে বাঙ্গালাদেশে ইংরাজ নীলকরের দ্বারা যে-সকল অত্যাচার ও অনাচার অনুষ্ঠিত হইত, তাহারই একটু আভাস দেওয়া। ইহারই অভিনয় ক্লাস হেট্রেড জাগিতে পারে, রাজশক্তির ইহাই আশঙ্কা। আশঙ্কা অমূলক বা সমূলক, এ আমার আলোচ্য নয়, কিংবা ইংরাজ নামের পরিবর্তে পর্তুগীজ নাম বসাইলে ক্লাস হেট্রেড বাঁচে কিনা সেও আমি জানি না,—ইংরাজের আইনে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে—কিন্তু যে আইন ইহারও উপরে, যাহাতে ‘ক্লাস’ বলিয়া কোন বস্তু নাই, তাহার নিরপেক্ষ বিচারে একের অপরাধ অপরের স্কন্ধে আরোপ করিলে যে বস্তু মরে, তাহার দাম ক্লাস হেট্রেডেরও অনেক বেশী। সেদিন দেখিলাম, এই ছোট ফাঁকিটুকু হইতে ছোটছেলেরাও অব্যাহতি পায় নাই। তাহাদের সামান্য পাঠ্যপুস্তকেও এই অসত্য স্থান লাভ করিয়াছে। নূতন গ্রন্থকার আমার মতামত জানিতে আসিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—এই আশ্চর্য নামটি আপনি সংগ্রহ করিলেন কিরূপে? গ্রন্থকার সলজ্জে কহিলেন—‘‘প্রাণের দায়ে করিতে হয়, মশাই! জানি সব, কিন্তু গরীব, পয়সা খরচা করিয়া বই ছাপাইয়াছি, তাই ওই ফন্দিটুকু না করিলে কোন স্কুলে এ বই চলিবে না।’’
তাঁহাকে আর কিছু বলিতে প্রবৃত্তি হইল না, কিন্তু মনে মনে নিজের কপালে করাঘাত করিয়া কহিলাম—যে-রাজ্যের শাসনতন্ত্রে সত্য নিন্দিত, যে-দেশের গ্রন্থকারকে জানিয়াও মিথ্যা লিখিতে হয়,—লিখিয়াও ভয়ে কণ্টকিত হইতে হয়, সে-দেশে মানুষে গ্রন্থকার হইতে চায় কেন? সে-দেশের অসত্য-সাহিত্য রসাতলে ডুবিয়া যাক না! সত্যহীন দেশের সাহিত্যে তাই আজ শক্তি নাই, গতি নাই, প্রাণ নাই। তাই আজ সাহিত্যের নাম দিয়া দেশে কেবল ঝুড়ি ঝুড়ি আবর্জনার সৃষ্টি হইতেছে। তাই আজ দেশের রঙ্গমঞ্চ ভদ্র-পরিত্যক্ত, পঙ্গু, অকর্মণ্য। সে না দেয় আনন্দ, না দেয় শিক্ষা। দেশের রক্তের সঙ্গে তাহার যোগ নাই, প্রাণের সঙ্গে পরিচয় নাই, দেশের আশা-ভরসার সে কেহ নয়—সে যেন, কোন্ অতীত যুগের মৃতদেহ। তাই পাঁচ শত বছর পূর্বে কবে কোন্ মোগল পাঠানকে জব্দ করিয়াছিল এবং কখন্ কোন্ সুযোগে মারহাট্টা রাজপুতকে মারিয়াছিল, সে শুধু ইহারই সাক্ষী, এ ছাড়া তাহার দেশের কাছে বলিবার আর কিছু নাই।
দেশের নাট্যকারগণের বুকের মধ্য হইতে যদি কখন সত্য ধ্বনিয়া উঠিয়াছে, আইনের নামে, শৃঙ্খলার নামে রাজসরকারে তাহা বাজেয়াপ্ত হইয়া গেছে; তাই সত্যবঞ্চিত নাট্যশালা আজ দেশের কাছে এমনই লজ্জিত, ব্যর্থ ও অর্থহীন। রুল ব্রিটানিয়া গাহিতে ইংরাজের বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠে, কিন্তু ‘আমার দেশ’ আমার দেশে নিষিদ্ধ। এই যে আজ আসমুদ্র-হিমাচল ব্যাপিয়া ভাবের বন্যা, কর্ম ও উদ্যমের স্রোত বহিতেছে, নাট্যাগারে তাহার এতটুকু স্পন্দন, এতটুকু সাড়া নাই। দেশের মাঝখানে বসিয়াও তাহার দরজা-জানালা ভয় ও মিথ্যার অর্গলে আজ এমনি অবরুদ্ধ যে, দেশজোড়া এতবড় দীপ্তির রশ্মিকণাটুকুও তাহাতে প্রবেশ করিবার পথ পায় নাই। কিন্তু কোন্ দেশে এমন ঘটিতে পারিত? আজ মাতৃভূমির মহাযজ্ঞে বুকের রক্ত যাঁহারা এমন করিয়া ঢালিয়া দিতেছেন, কোন্ দেশের নাট্যশালা হইতে তাঁহাদের নাম পর্যন্ত আজ এমন করিয়া বারিত হইতে পারিত! অথচ সমস্তই দেশেরই কল্যাণের নিমিত্ত। দেশের কল্যাণের জন্যই আজ দেশের নাট্যকারগণের কলমের গাঁটে গাঁটে আইনের ফাঁস বাঁধা। এবং এমন কথাও আজ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইতেছে যে, দেশের কবি, দেশের নাট্যকারগণের অন্তর ভেদিয়া যে বাক্য, যে সঙ্গীত বাহির হইয়া আসে, দেশের তাহাতে কল্যাণ নাই, শক্তি নাই। বিদেশী রাজপুরুষের মুখ হইতে এ কথাও আজ আমাদের মানিয়া চলিতে হইতেছে। কিন্তু এই নির্বিচারে মানিয়া চলার লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশের আজ সময় আসিয়াছে। এবং ইহা কি শুধু একা আমাদেরই ক্ষুদ্র করিয়া রাখিয়াছে? যে ইহা চালাইতেছে, সে ছোট রয় নাই? আমরা দুঃখ পাইতেছি, কিন্তু মিথ্যাকে সত্য করিয়া দেখাইবার দুঃখভোগ সে-ই কি চিরদিন এড়াইয়া যাইবে? ঋণ-পরিশোধের দুঃখ আছে,—আজ আমাদের ডাক পড়িয়াছে, কিন্তু দেনা শোধ করিবার তলব যেদিন তাহারও ভাগ্যে আসিবে, সেদিন তাহারই কি মুখে হাসি ধরিবে না?
ব্যাপারটা কাগজে-কলমে লোকের চোখে কি ঠেকিতেছে, ঠিক জানি না। হয়ত এই বাঙ্গলাদেশেই এমন মানুষও আছেন, যাঁহাদের কাছে আগাগোড়া তুচ্ছ মনে হওয়াও বিচিত্র নয়;এবং যদি তাই হয়, তবুও আরও এমনি একটা তুচ্ছ ঘটনার উল্লেখ করিয়াই এ প্রসঙ্গ এবারের মত বন্ধ করিব।
সেদিন University Institute- এ ছেলেদের মধ্যে কবিতা আবৃত্তির একটা প্রতিযোগিতার পরীক্ষা ছিল। সর্বদেশপূজিত কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘এবার ফিরাও মোরে’ শীর্ষক কবিতাটি নির্বাচিত করা হইয়াছিল। যাহারা পরীক্ষা দিবে, তাহাদেরই একজন আমার কাছে দুই-একটা কথা জানিয়া লইতে আসিয়াছিল। তাহারই কাছে দেখিয়া অবাক হইয়া গেলাম যে, এই সুদীর্ঘ কবিতাটির যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ,—এই দুর্ভাগা দেশের দুর্দশার কাহিনী যেথায় বিবৃত—সেই অংশগুলিই বাছিয়া বাছিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ কুকার্য কে করিল?
ছেলেটি কহিল, আজ্ঞে, নির্বাচনের ভার যাঁহাদের উপর ছিল, তাঁহারা।
মনে করিলাম, রত্ন ইঁহারা চিনেন না, তাই, এও বুঝি সেই ছোবড়া-আঁটির ব্যাপার হইয়াছে। কিন্তু ছেলেটি দেখিলাম সব জানে, সে আমার ভুল ভাঙ্গিয়া দিল। সবিনয়ে কহিল, আজ্ঞে, তাঁরা সমস্তই জানেন, তবে কিনা ওতে দেশের দুঃখ-দৈন্যের কথা আছে, তাই ওটা আবৃত্তি করা যায় না—ওটা সিডিশন।
কহিলাম—কে বলিল?
ছেলেটি জবাব দিল—আমাদের কর্তৃপক্ষরা।
যাক,—বাঁচা গেল। কর্তৃপক্ষ এদিকেও আছেন। অর্বাচীন শিশুগুলার মঙ্গল-চিন্তা করিতে এ-পক্ষেও পাকা মাথার অভাব ঘটে নাই। প্রশ্ন করিলাম—আচ্ছা তোমরা এই কবিতাংশগুলি সভায় আবৃত্তি করিতে পার না?
সে কহিল, পারি, কিন্তু তাঁরা বলেন, পারা উচিত নয়,ফ্যাসাদ বাধিতে পারে।
আর প্রশ্ন করিতে প্রবৃত্তি হইল না। দেশের যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি, যিনি নিষ্পাপ, নির্মল—স্বদেশের হিতার্থে যে কবিতা তাঁহার অন্তর হইতে উত্থিত হইয়াছে, প্রকাশ্য সভায় তাহার আবৃত্তি সিডিশন—তাহা অপরাধের! এবং এই সত্য দেশের ছেলেরা আজ কর্তৃপক্ষের কাছে শিক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছে। এবং কর্তৃপক্ষের অকাট্য যুক্তি এই যে,—ফ্যাসাদ বাধিতে পারে। (‘বাঙলার কথা,’ ২০ই মাঘ ও ৫ ফাল্গুন ১৩২৮)
সত্যাশ্রয়ী
ছাত্র, যুবক ও সমবেত বন্ধুগণ,—বাংলাভাষায় শব্দের অভাব ছিল না; অথচ, এই আশ্রমের যাঁরা প্রতিষ্ঠাতা, তাঁরা বেছে বেছে এর নাম দিয়েছিলেন ‘অভয় আশ্রম’। বাইরের লোকসমাজে প্রতিষ্ঠানটিকে অভিহিত করার নানা নামই ত ছিল, তবু তাঁরা বললেন—অভয় আশ্রম। বাইরের পরিচয়টা গৌণ, মনে হয় যেন সঙ্ঘ স্থাপনা করে বিশেষভাবে তাঁরা নিজেদেরই বলতে চেয়েছিলেন—স্বদেশের কাজে যেন আমরা নির্ভয় হতে পারি, এ জীবনের যাত্রাপথে যেন আমাদের ভয় না থাকে। সর্বপ্রকার দুঃখ, দৈন্য ও হীনতার মূলে মনুষ্যত্বের চরম শত্রু ভয়কে উপলব্ধি করে বিধাতার কাছে তাঁরা অভয় বর প্রার্থনা করে নিয়েছিলেন। নামকরণের ইতিহাসে এই তথ্যটির মূল্য আছে; এবং আজ আমার মনের মধ্যে কোন সংশয় নেই যে, সে আবেদন তাঁদের বিধাতার দরবারে মঞ্জুর হয়েছে। কর্মসূত্রে এঁদের সঙ্গে আমার অনেকদিনের পরিচয়। দূরে থেকে সামান্য যা-কিছু বিবরণ শুনতে পেতাম, তার থেকে মনের মধ্যে আমার এই আকাঙ্ক্ষা প্রবল ছিল—একবার নিজের চোখে গিয়ে সমস্ত দেখে আসব। তাই, আমার পরম প্রীতিভাজন প্রফুল্লচন্দ্র যখন আমাকে সরস্বতীপূজা উপলক্ষে এখানে আহ্বান করলেন, তাঁর সে আমন্ত্রণ আমি নিরতিশয় আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করলাম। শুধু একটি মাত্র শর্ত করিয়ে নিলাম যে, অভয় আশ্রমের পক্ষ থেকে আমাকে অভয় দেওয়া হোক যে, মঞ্চে তুলে দিয়ে আমাকে অসাধ্য-সাধনে নিযুক্ত করা হবে না। বক্তৃতা দেবার বিভীষিকা থেকে আমাকে মুক্তি দেওয়া হবে। জীবনে যদি কিছুকে ভয় করি ত একেই করি। তবে এটুকুও বলেছিলাম—যদি সময় পাই ত দু-এক ছত্র লিখে নিয়ে যাব। সে লেখা প্রয়োজনের দিক থেকেও যৎসামান্য, উপদেশের দিক দিয়েও অকিঞ্চিৎকর। ইচ্ছে ছিল, কথার বোঝা আর না বাড়িয়ে উৎসবের মেলামেশায় আপনাদের কাছ থেকে আনন্দের সঞ্চয় নিয়ে ঘরে ফিরব। আমি সে সঙ্কল্প ভুলিনি এবং এই দু-দিনে সঞ্চয়ের দিক থেকেও ঠকিনি। কিন্তু এ আমার নিজের দিক। বাইরেও একটা দিক আছে, সে যখন এসে পড়ে, তার দায়িত্বও অস্বীকার করা যায় না। তেমনি এলো প্রফুল্লচন্দ্রের ছাপানো কার্য-তালিকা। রওনা হতে হবে, সময় নেই,—কিন্তু পড়ে দেখলাম, অভয় আশ্রম পশ্চিম-বিক্রমপুর-নিবাসী ছাত্র ও যুবকদের মিলনক্ষেত্রের আয়োজন করেছে। ছেলেরা এখানে সমবেত হবেন। তাঁরা আমাকে অব্যাহতি দেবেন না; বলবেন,—কিশোর বয়স থেকে ছাপা-বইয়ের ভিতর দিয়ে আপনার অনেক কথা শুনেছি, আজও যখন কাছে পেয়েছি, তখন যা হোক কিছু না শুনে ছাড়ব না। তারই ফলে এই কয়েক ছত্র আমার লেখা। মনে হবে তা বেশ ত, কিন্তু এতবড় ভূমিকার কি আবশ্যক ছিল? তার উত্তরে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ভিতরের বস্তু যখন কম থাকে, তখন মুখবন্ধের আড়ম্বর দিয়েই শ্রোতার মুখ বন্ধের প্রয়োজন হয়।
নিজের চিন্তাশীলতায় নূতন কথা বলবার আমার শক্তি-সামর্থ্য কিছুই নাই, স্বদেশবৎসল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের মুখে বহু সভা-সমিতিতে যে-সকল কথা আপনারা বহুবার শুনেছেন, আমি সেই সবই শুধু লিপিবদ্ধ করে এনেছি। ভেবেছি, অভিনবত্ব নাই থাক, মৌলিকত্ব যত বড় হোক, তার চেয়েও বড় সত্য কথা। পুরানো বলে সে তুচ্ছ নয়, তাকে আর একবার স্মরণ করিয়ে দেওয়াও বড় কাজ। তেমনি মাত্র গুটি দুই-তিন কথাই আজ আমি আপনাদের কাছে উল্লেখ করব।
কিছুদিন থেকে একটা বিষয় আমি লক্ষ্য করে আসছি। ভাবি, এতবড় সত্যটা এতকাল গোপনে ছিল কি করে? সেদিনও সবাই জানত, সবাই মানত—পলিটিক্স জিনিসটা কেবল বুড়োদেরই ইজারা মহল। আবেদন-নিবেদন, মান-অভিমান থেকে শুরু করে চোখ-রাঙ্গানো পর্যন্ত বিদেশী রাজশক্তির সঙ্গে যা-কিছু মোকাবিলার দায়িত্ব, সব তাদের। ছেলেদের এখানে একেবারে প্রবেশ নিষেধ। শুধু অনধিকার-চর্চা নয়, গর্হিত অপরাধ। তারা ইস্কুল-কলেজে যাবে, শান্তশিষ্ট ভাল ছেলে হয়ে পাস করে বাপ-মায়ের মুখোজ্জ্বল করবে—এই ছিল সর্ববাদিসম্মত ছাত্র-জীবনের নীতি। এর যে কোন ব্যত্যয় ঘটতে পারে, এর বিরুদ্ধে যে প্রশ্ন মাত্র উঠতে পারে, এ ছিল যেন লোকের স্বপ্নাতীত। হঠাৎ কোথাকার কোন্ উলটো ঝোড়ো হাওয়ায় এর কেন্দ্রটাকে ঠেলে নিয়ে একেবারে যেন পরিধির বাইরে ফেলে দিলে। বিদ্যুৎ-শিখা যেমন অকস্মাৎ ঘনান্ধকারের বুক চিরে বস্তুর প্রকাশ করে, নৈরাশ্য ও বেদনার অগ্নি-শিখা তেমনি করেই আজ সত্য উদ্ঘাটিত করেছে। যা চোখের অন্তরালে ছিল, তা দৃষ্টির সুমুখে এসে পড়েছে। সমস্ত ভারতবর্ষময় কোথাও আজ সন্দেহের লেশমাত্র নেই যে, এতদিন লোকে যা ভেবে এসেছে তা ভুল, সত্য তাতে ছিল না বলেই বিধাতা বারংবার ব্যর্থতার কালিমা দেশের সর্বাঙ্গে মাখিয়ে দিয়েছেন। এ গুরুভার বৃদ্ধদের জন্যে নয়, এ ভার যৌবনের। তাই ত আজ ইস্কুল-কলেজে, নগরে-পল্লীতে, ভারতের প্রত্যেক ঘরে ঘরে যৌবনের ডাক পড়েছে। ডাক বৃদ্ধরা দেয়নি, দিয়েছেন বিধাতাপুরুষ নিজে। তাঁর আহ্বান কানের মধ্যে দিয়ে এদের বুকে পৌঁছেছে যে, জননীর হাতে-পায়ে বাঁধা এই কঠিন শৃঙ্খল ভাঙ্গবার শক্তি অতি প্রাজ্ঞ প্রবীণের হিসাবী বুদ্ধির মধ্যে নেই, এই শক্তি আছে শুধু যৌবনের প্রাণচঞ্চল হৃদয়ের মধ্যে। এই নিঃসংশয় আত্মবিশ্বাসে আজ তাকে প্রতিষ্ঠিত হতেই হবে। এতদিন বিদেশীয় বণিক রাজশক্তির কোন চিন্তাই ছিল না, বৃদ্ধের রাজনীতি চর্চাকে সে খেলাচ্ছলেই গ্রহণ করে এসেছিল, কিন্তু এখন তার আর খেলার অবকাশ নেই। দিকে দিকে এ চিহ্ন কি আপনাদের চোখে পড়েনি? যদি না পড়ে থাকে, চোখ মেলে চেয়ে দেখতে বলি। রাজশক্তি আজ ব্যাকুল এবং অচিরভবিষ্যতে এই অন্ধ-ব্যাকুলতায় দেশ ছেয়ে যাবে—এ সত্যও আজ আপনাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে বলি। আরও বলি, সেদিন যেন এই সত্যোপলব্ধির অবমাননা না ঘটে।
এখানে একটা কথা বলে রাখি। কারণ, সন্দেহ হতে পারে, সর্বদেশেই ত রাজনীতি পরিচালনার ভার বৃদ্ধদের স্কন্ধে ন্যস্ত থাকে, কিন্তু এখানে তার অন্যথা হবে কেন? অন্যথা এখানেও হবে না, একদিন তাঁদের ‘পরেই রাজ্যশাসনের দায়িত্ব পড়বে। কিন্তু সেদিন আজ নয়। এখনও সে এসে পৌঁছয় নি। কারণ, দেশ শাসন করা ও স্বাধীন করা এক বস্তু নয়। এ কথা মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন যে, রাজনীতি-পরিচালনা একটা পেশা। যেমন ডাক্তারি, ওকালতি, প্রফেসারি,—এমনি। অন্যান্য সমুদয় বিদ্যার মত একেও শিক্ষা করতে হয়, আয়ত্ত করতে সময় লাগে। তর্কের মার-প্যাঁচ, কথা-কাটাকাটির লড়াই, আইনের ফাঁক খুঁজে কড়া করে দু-কথা শুনিয়ে দেওয়া,—আবার যথাসময়ে আত্মসংবরণ ও বিনীত ভাষণ,—এ-সকল কঠিন ব্যাপার, এবং বয়স ছাড়া এতে পারদর্শিতা জন্মে না। এরই নাম পলিটিক্স। স্বাধীন দেশে এর থেকে জীবিকা-নির্বাহ চলে। কিন্তু পরাধীন দেশে সে ব্যবস্থা নয়। সেখানে দেশের মুক্তি-অর্জন-পথে পদে পদে আপনাকে বঞ্চিত করে চলতে হয়ে। এ ত তার পেশা নয়, এ তার ধর্ম। তাই, এই পরম ত্যাগের ব্রত শুধু যৌবনই গ্রহণ করতে পারে। এ তার স্বাধিকার- চর্চা, অনধিকার-চর্চা নয় বলেই রাজশক্তি একে ভয়ের চক্ষে দেখতে আরম্ভ করেছে। এ-ই স্বাভাবিক, এবং এর গতিপথে বাধার অবধি থাকবে না, এ-ও তেমনি স্বাভাবিক। কিন্তু এই সত্যটাকে ক্ষোভের সঙ্গে নয়, আনন্দের সঙ্গেই মেনে নিয়ে অগ্রসর হতে আজ আপনাদের আমি আহ্বান করি।
শব্দের ঘটায় ও বাক্যের ছটায় উত্তেজনার সৃষ্টি করতে আমি অপারক। শান্ত-সমাহিত চিত্তে সত্যোপলব্ধি করতেই আমি অনুরোধ করি। আমরা আত্মবিস্মৃত জাতি, আমাদের এই ছিল, এই ছিল, এই ছিল এবং এই আছে, এই আছে, এই আছে—সুতরাং ঘুম ভেঙ্গে চোখ রগড়ে উঠে বসলেই সব পাব, এ যাদুবিদ্যার আশ্বাস দিতে আমার কোন কালেই প্রবৃত্তি হয় না। জগৎ মানুক আর না মানুক, আমরা মস্ত বড় জাতি, এ কথা বহু আস্ফালনে দিকে দিকে ঘোষণা করে বেড়াতেও যেমন আমি গৌরব বোধ করিনে, তেমনি, বিদেশী রাজশক্তিকেও ধিক্কার দিয়ে ডেকে বলতে লজ্জা বোধ করি যে, হে ইংরাজ, তোমরা কিছুই নয়, কারণ, অতীতকালে আমরা যখন এই এই মস্ত বড় বড় কাজ করেছি, তোমরা তখন শুধু গাছের ডালে ডালে বেড়াতে।
এবং বিদ্রূপ করে কেউ যদি আমাকে বলে—তোমরা যদি সত্যই এত বড়, তবে হাজার বছর ধরে একবার পাঠান, একবার মোগল, একবার ইংরাজের পায়ের তলে তোমাদের মাথা মুড়োয় কেন, তবে এ উপহাসের প্রত্যুত্তরেও আমি ইতিহাসের পুঁথি ঘেঁটে অন্যান্য জাতির দুর্দশার নজির দেখাতেও ঘৃণা বোধ করি। বস্তুতঃ এ তর্কে লাভ নেই। বিগত দিনে তোমার আমার কি ছিল, এ নিয়ে গ্লানি বাড়িয়ে কি হবে,—আমি বলি, ইংরাজ, আজ তুমি বড়; শৌর্যে, বীর্যে, স্বদেশপ্রেমে তোমার জোড়া নেই; কিন্তু আমারও বড় হবার সমস্ত মালমশলা মজুত। আজ দেশের যৌবন-চিত্ত পথের খোঁজে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, তাকে ঠেকাবার শক্তি কারও নেই, তোমারও না। তুমি যত বড়ই হও, সে তোমারই মত বড় হয়ে তার জন্মের অধিকার আদায় করে নেবেই নেবে।
কিন্তু কোন্ সংজ্ঞায় যৌবনকে নির্দেশ করা যায়? অতীত যার কাছে অতীতের বেশী নয়, সে যত বৃহৎ হোক, মুগ্ধ-চিত্ত তলে তাকেই লালন করে কালক্ষেপের অবসর যার নেই, যার বৃহত্তর আশা ও বিশ্বাস অনাগতের অন্তরালে কল্পনায় উদ্ভাসিত—সেই ত যৌবন। এখানেই বৃদ্ধের পরাজয়। শক্তি তার নিঃশেষিতপ্রায়, ভবিষ্যৎ আশাহীন শুষ্ক, সম্মুখ অবরুদ্ধ, শেষ জীবনের বাকী দিন-ক’টা তাই প্রাণপণে অতীতকে আঁকড়ে থাকাই তার সান্ত্বনা। এ অবলম্বন সে কোন মতেই ছাড়তে পারে না, কেবলই ভয় হয়, এর থেকে বিচ্যুত হলে তার দাঁড়াবার স্থান আর কোথাও থাকবে না। স্থিতিশীল শান্তিই তার একান্ত আশ্রয়, বহুদিন আবদ্ধ খাঁচার পাখির মত, মুক্তিই তার বন্ধন, মুক্তিই তার সুনিয়ন্ত্রিত অভ্যাসসিদ্ধ প্রাণধারণ-প্রণালীর যথার্থ অন্তরায়। এইখানেই যৌবনের সঙ্গে তার প্রচণ্ড বিভেদ। দেশের সমাজের জাতির মুক্তি-বিধানের দায়িত্ব যতদিন এই বৃদ্ধদের হাতেই থাকবে, বন্ধনের গ্রন্থিতে পাকের পর পাক পড়তেই থাকবে, খুলবে না। কিন্তু যৌবন-ধর্ম এর বিপরীত। তাই যেদিন থেকে শুনতে পেলাম, স্কুল-কলেজের ছাত্র আর রাজনীতিকে—যে রাজনীতি কেবল মাত্র পলিটিক্স নয়, যে রাজনীতি স্বদেশের মুক্তিযজ্ঞে ব্রতের মত, ধর্মের মত, তাকেই গ্রহণ করতে বদ্ধপরিকর হয়ছে, এ কুসংস্কারের হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে যে, এ বস্তু তার ছাত্রজীবনের পরিপন্থী—সেইদিনই আমার প্রতীতি জন্মেছে, এবার সত্য সত্যিই আমাদের দুর্গতি মোচন হবে। ছাত্র এবং দেশের যুবক-সম্প্রদায়ের কাছে আমার অন্তরের নিবেদন, এ সঙ্কল্প থেকে যেন তাঁরা কারও কথায় কোন প্রলোভনেই বিচ্যুত না হন।
এ সম্বন্ধে বহু মনীষী ব্যক্তিই বহু উপদেশ দিয়েছেন। তোমরা এই কর, এই কর, এই কর,—এই তোমাদের করণীয়, এই আচরণই প্রশস্ত, স্বার্থত্যাগ চাই, বুকের মধ্যে স্বদেশ-প্রীতি জ্বালিয়ে তোলা প্রয়োজন, জাতি-ভেদ অস্বীকার, ছুঁৎমার্গ পরিহার, খদ্দর পরিধান—এমনি অনেক আবশ্যকীয় ও মূল্যবান আদেশ এবং উপদেশ। এই হলো প্রোগ্রাম। আবার অন্যপ্রকার উপদেশ, ভিন্ন প্রোগ্রামও আছে। আপনাদেরই মত দেশের বহু ছাত্র ও যুবক আমাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন—আমরা কি করব আপনি বলে দিন। উত্তরে আমি বলি,—প্রোগ্রাম ত আমি দিতে পারিনে, আমি শুধু তোমাদের বলতে পারি, তোমরা দৃঢ়পণে ‘সত্যাশ্রয়ী’ হও। তাঁরা প্রশ্ন করেন, এ ক্ষেত্রে সত্য কি? বিভিন্ন মতামত ও প্রোগ্রাম যে আমাদের উদ্ভ্রান্ত করে দেয়। জবাবে আমি বলি, সত্যের কোন শাশ্বত সংজ্ঞা আমার জানা নেই। দেশ, কাল ও পাত্রের সম্বন্ধ বা relation দিয়েই সত্যের যাচাই হয়। দেশ কাল পাত্রের পরস্পরের সম্বন্ধের সত্যজ্ঞানই সত্যের স্বরূপ। একের পরিবর্তনের সঙ্গে অপরের পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্তন বুদ্ধিপূর্বক মেনে নেওয়াই সত্যকে জানা। যেমন বহু পূর্বকালে রাজাই ছিলেন ভগবানের প্রতিনিধি। দেশের লোকে এ কথা মেনে নিয়েছিল। একে অসত্য বলতে আমি চাইনে। সেই প্রাচীন যুগে হয়ত এই ছিল সত্য, কিন্তু আজ জ্ঞান ও পারিপার্শ্বিকের পরিবর্তনের ফলে এ কথা যদি ভ্রান্ত বলেই প্রমাণিত হয়, তবুও কোন এক সাবেক দিনের যুক্তি ও উক্তি-মাত্রকেই অবলম্বন করে একেই সত্য বলে যদি কেউ তর্ক করে, তাকে আর যাই কেন না বলি, ‘সত্যাশ্রয়ী’ বলব না। কিন্তু শুদ্ধমাত্র মানাই এর সবটুকু নয়,—বস্তুতঃ, আর একদিক দিয়ে কোন সার্থকতাই এর নেই—যদি না চিন্তায়, বাক্যে ও ব্যবহারে, জীবনযাত্রার পদে পদে এ সত্য বিকশিত হয়ে ওঠে। ভুল জানা, ভ্রান্ত ধারণা, বরঞ্চ সেও ভালো, কিন্তু ভিতরের জানা ও বাইরের আচরণে যদি সামঞ্জস্য না থাকে,—অর্থাৎ যদি জানি একরকম, বলি আর একরকম এবং করি আর একরকম,—তবে জীবনের এতবড় ব্যর্থতা এতবড় ভীরুতা আর নেই। যৌবন-ধর্মকে এতখানি ছোট করতে আর দ্বিতীয় কিছু নেই। ছুঁৎমার্গ, জাতিভেদ, খদ্দর পরিধান, জাতীয় শিক্ষা, দেশের কাজ—এ-সব সত্য কি অসত্য, ভাল কি মন্দ, এ আলোচনা আমি করব না, এর সত্যাসত্য বুঝিয়ে দেবার আমার চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি আপনারা অনেক পাবেন, কিন্তু আমি কেবল এই নিবেদনই করব, আপনাদের বুঝার সঙ্গে যেন কার্যের ঐক্য থাকে।
বুঝি, ছোঁয়াছুঁয়ি আচার-বিচারের অর্থ নেই, তবু মেনে চলি; বুঝি, জাতিভেদ মহা-অকল্যাণকর, তবু নিজের আচরণে তাকে প্রকাশ করিনে, বুঝি ও বলি, বিধবা-বিবাহ উচিত তবু নিজের জীবনে তাকে প্রত্যাহার করি, জানি খদ্দর পরা উচিত, তবু বিলাতী কাপড় পরি, একেই বলি আমি অসত্যাচরণ। দেশের দুর্দশা ও দুর্গতির মূলে এই মহাপাপ যে আমাদের কতখানি নীচে টেনে এনেছে, এ হয়ত আমরা কল্পনাও করিনে। এমনিধারা সকল দিকে। দৃষ্টান্ত দিয়ে সময় অতিবাহিত করবার প্রয়োজন নেই—প্রার্থনা, দীনতা ও কাপুরুষতার এই গভীর পঙ্ক থেকে দেশের যৌবন যেন মুক্তিলাভ করতে পারে। ভুল বুঝে ভুল কাজ করায় অজ্ঞতার অপরাধ হয়, সেও ঢের ভাল, কিন্তু ঠিক বুঝে বেঠিক কাজ করায় শুধু সত্যভ্রষ্টতার নয়, অসত্যনিষ্ঠার প্রত্যবায় হয়। তার প্রায়শ্চিত্তের যখন দিন আসে, তখন সমস্ত দেশের শক্তিতে কুলোয় না। এ কথা মনে রাখতে হবে, সত্যনিষ্ঠাই শক্তি, সত্যনিষ্ঠাই সমস্ত মঙ্গলের আধার এবং ইংরাজিতে যাকে বলে tenacity of purpose, সেও এই সত্যনিষ্ঠারই বিকাশ। তাই বারংবার স্বদেশের যৌবনের কাছে এই আবেদনই করি, সত্য-নিষ্ঠাই যেন তাদের ব্রত হয়। কেন না, নিশ্চয় জানি এই ব্রতধারণই তাদের সম্মুখের সমস্ত বাধা অপসারণ করে যথার্থ কল্যাণের পথ উদ্ঘাটিত করে দেবে। প্রোগ্রাম ও পথের জন্য দুশ্চিন্তা করতে হবে না।
আজকের কার্য-তালিকায় একটা বিষয় আছে, সে হচ্ছে লাঠি, তলোয়ার ও ছোরা খেলা। এতদিন physical culture-এর দিকে ছাত্রসমাজ একেবারে বিমুখ হয়ে পড়েছিল। মনে হয়, এইটে ধীরে ধীরে আবার যেন ফিরে আসছে। এই প্রত্যাগমনকে আমি সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করি। তারা দেখেছে, দুর্বল শক্তিহীনেরই শুধু লাথির ঘায়ে প্লীহা ফাটে। শক্তিমান পাঠান-কাবলীওয়ালার ফাটে না। ফাটে বাঙ্গালীর। বোধ হয় বারংবার এই ধিক্কারেই শারীরিক শক্তি অর্জনের স্পৃহা ফিরে এলো। physical culture-এ শক্তি বাড়ে, আত্মরক্ষার কৌশল আয়ও হয়, সাহস বৃদ্ধি পায়—কিন্তু তবুও এ কথা ভুললে চলবে না যে, এ সমস্তই দেহের ব্যাপার। অতএব এই-ই সবটুকু নয়। সাহস বাড়া এবং নির্ভীকতা অর্জন কোনমতেই এক বস্তু নয়। একটা দৈহিক, অন্যটা মানসিক।
দেহের শক্তি ও কৌশল-বৃদ্ধিতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও অকৌশলীকে পরাভূত করা যায়, কিন্তু নির্ভয়ের সাধনায় শক্তিমানকে পরাস্ত করা যায়,—সংসারে কেউ তাকে বাধা দিতে পারে না, সে হয় অপরাজেয়। তাই প্রারম্ভে যে কথা একবার বলেছি, তাই পুনরুক্তি করে আবার বলি যে, এই অভয় আশ্রম সেই সাধনাতেই নিযুক্ত। এঁদের কৃচ্ছ্রসাধনা তারই একটা সোপান, একটা উপায়। এ তাঁদের পথ, শেষ লক্ষ্য নয়। অভাব, দুঃখ, ক্লেশ, প্রতিবেশীর লাঞ্ছনা, বন্ধুজনের গঞ্জনা, প্রবলের উৎপীড়ন, কোন কিছুই যেন এঁদের মুক্তির পথকে বাধাগ্রস্ত না করতে পারে—এ-ই এঁদের একান্ত পণ। এই ত নির্ভয়ের সাধনা এবং তাই সত্যনিষ্ঠাই এঁদের গন্তব্য-পথকে নিরন্তর আলোকিত করে চলেছে। খদ্দর প্রচার, জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, হাসপাতাল খোলা, আর্তের সেবা, এ-সব ভাল কি মন্দ, নির্ভীকতা ও দেশের স্বাধীনতা অর্জনে এ-সমস্ত কাজের কি না,—এ-সব প্রশ্ন বৃথা! এঁদের সত্যনিষ্ঠা কাল যদি এঁদের চক্ষে অন্য পথ নির্দেশ করে, এই সমস্ত আয়োজন নিজের হাতে ভেঙ্গে ফেলতে অভয় আশ্রমীদের একমুহূর্ত বিলম্ব হবে না—এই আমার বিশ্বাস। এবং কামনা করি, এ বিশ্বাস যেন আমার সত্য হয়।
আমার বয়েস অনেক হলো, তবু এখানে এসে অনেক কিছুই শিখলাম। এই অভয় আশ্রমে অতিথি হতে পারার সৌভাগ্য আমার শেষদিন পর্যন্ত মনে থাকবে।
পরিশেষে, এই ছাত্র ও যুব-সঙ্ঘকে আশীর্বাদ করি, যেন এঁদের মতই সত্যনিষ্ঠা তাঁদেরও জীবনের ধ্রুবতারা হয়।
আপনারা আমার সকৃতজ্ঞ অন্তরের নমস্কার গ্রহণ করুন।
সধবার একাদশী
এই সুপরিচিত গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখিতে যাওয়াই বোধ করি একটা বাড়াবাড়ি। অথচ, এই কাজের জন্যই আমি অনুরুদ্ধ হইয়াছি। খুব সম্ভব, আমাকেই ইঁহারা যোগ্য ব্যক্তি কল্পনা করিয়া লইয়াছেন।
যে বইয়ের দোষ-গুণ আজ অর্ধ শতাব্দী কাল ধরিয়া যাচাই হইতেছে,—বিশেষত, যে মারাত্মক উৎপাত কাটাইয়া সম্প্রতি ইহা খাড়া হইয়া উঠিল, তাহাতে মূল্য লইয়া ইহার আর দরদস্তুর করা সাজে না। বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাণ্ডারে এ একখানি জাতীয় সম্পত্তি—এ সত্য মানিয়া লওয়াই ভাল।
অতএব, গ্রন্থ সম্বন্ধে নয়, আমি ইহার সংস্করণ সম্বন্ধেই দুই-একটা কথা বলিব।
অত্যন্ত দুর্দিনে দেশের অনেক বহুমূল্য বস্তুই বটতলার সংস্করণ সঞ্জীবিত রাখিয়াছে,—তাই আজ তাহাদের অনেকেরই ভদ্র সাজসজ্জা সম্ভবপর হইতে পারিয়াছে, এবং বাঙ্গালীর সম্পত্তি বলিয়াও গণ্য হইয়াছে।
জানি না, ইহারও কোন দিন বটতলার ছায়ায় মাথা বাঁচাইবার প্রয়োজন ঘটিয়াছে কি না, কিন্তু আমার বক্তব্য শুধু এই যে, যে-কোন সংস্করণই এত দিন যাবৎ ইহার প্রাণ বাঁচাইয়া আসিয়াছে, তাহার যত দোষ যত ত্রুটিই থাক, সে কেবল আমাদের কৃতজ্ঞতা নয়, ভক্তিরও পাত্র।
অথচ, শুনিতেছি, বাঙ্গালা সাহিত্যের সে দুঃসময় আর নাই, তাই দুঃখ যদি আজ সত্যই ঘুচিয়া থাকে ত, যে-সকল গ্রন্থ আমাদের ঐশ্বর্য, আমাদের গৌরব, তাহাদের মলিন জীর্ণ-বাস ঘুচাইবারও প্রয়োজন হইয়াছে।
প্রকাশক বলিতেছেন, সেই উদ্দেশ্যেই এই নির্ভুল সুন্দর সংস্করণ, এবং একখানি মাত্র বই-ই তাঁহাদের প্রথম ও শেষ উদ্যম নয়।
উদ্দেশ্য সাধু, এবং প্রার্থনা করি, ইহা জয়যুক্ত হউক, কিন্তু ইহাও জানি, প্রকাশক কেবল সঙ্কল্প করিতেই পারেন, কিন্তু ইহার স্থায়িত্ব ও সিদ্ধি যাহাদের হাতে, সেই দেশের পাঠক-পাঠিকা যদি না চোখ মেলিয়া চান ত, কিছুতেই কিছু হইবে না। কিন্তু, এত বড় কলঙ্কের কথাও আমার ভাবিতে ইচ্ছা করে না।
বিলাত প্রভৃতি অঞ্চলে Oxford Press ‘World’s Classics’ নাম দিয়া একটির পরে একটি যে-সকল অমূল্য গ্রন্থরাজি প্রকাশ করিতেছেন, তাহারই সহিত এই নব-সংস্করণের একটা তুলনা করিবার কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু আমি বলি—আজ নয়।
হয়ত, অনতিকাল মধ্যেই একদিন তাহার সময় আসিবে, কিন্তু তখন বাঙ্গালা দেশকে সে শুভ সংবাদ নিবেদন করিতে যোগ্যতর ব্যক্তিরও অভাব হইবে না। শিবপুর, ৬ই ফাল্গুন ১৩২৬।*
সমাজ-ধর্মের মূল্য
বিড়ালকে মার্জার বলিয়া বুঝাইবার প্রয়াস করায় পাণ্ডিত্য প্রকাশ যদি বা পায়, তথাপি পণ্ডিতের কাণ্ডজ্ঞান সম্বন্ধে লোকের যে দারুণ সংশয় উপস্থিত হইবে, তাহা আমি নিশ্চয় জানি। জানি বলিয়াই, প্রবন্ধ লেখার প্রচলিত পদ্ধতি যাই হউক, প্রথমেই ‘সমাজ’ কথাটা বুঝাইবার জন্য ইহার ব্যুৎপত্তিগত এবং উৎপত্তিগত ইতিহাস বিবৃত করিয়া, বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া, অবশেষে ইহা এ নয়, ও নয়, তা নয়—বলিয়া পাঠকের চিত্ত বিভ্রান্ত করিয়া দিয়া গবেষণাপূর্ণ উপসংহার করিতে আমি নারাজ। আমি জানি, এ প্রবন্ধ পড়িতে যাঁহার ধৈর্য থাকিবে, তাঁহাকে ‘সমাজের’ মানে বুঝাইতে হইবে না। দলবদ্ধ হইয়া বাস করার নামই যে সমাজ নয়—মৌরোলা মাছের ঝাঁক, মৌমাছির চাক, পিঁপড়ার বাসা বা বীর হনুমানের মস্ত দলটাকে যে ‘সমাজ’ বলে না, এ খবর আমার নিকট হইতে এই তিনি নূতন শুনিবেন না।
তবে, কেহ যদি বলেন, ‘সমাজ’ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ঝাপসা গোছের ধারণা মানুষের থাকিতে পারে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সূক্ষ্ম অর্থ প্রকাশ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করা কি প্রবন্ধকারের উচিত নয়? তাঁহাদের কাছে আমার বক্তব্য এই যে, না। কারণ সংসারে অনেক বস্তু আছে, যাহার মোটামুটি ঝাপসা ধারণাটাই সত্য বস্তু,—সূক্ষ্ম করিয়া দেখাইতে যাওয়া শুধু বিড়ম্বনা নয়, ফাঁকি দেওয়া ! ‘ঈশ্বর’ বলিলে যে ধারণাটা মানুষের হয়, সেটা অত্যন্তই মোটা, কিন্তু সেইটাই কাজের জিনিস। এই মোটার উপরেই দুনিয়া চলে, সূক্ষ্মের উপর নয়। সমাজও ঠিক তাই। একজন অশিক্ষিত পাড়াগাঁয়ের চাষা ‘সমাজ’ বলিয়া যাহাকে জানে, তাহার উপরেই নির্ভয়ে ভর দেওয়া চলে—পণ্ডিতের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যাটির উপরে চলে না। অন্ততঃ আমি বোঝাপড়া করিতে চাই এই মোটা বস্তুটিকে লইয়াই। যে সমাজ মড়া মরিলে কাঁধ দিতে আসে, আবার শ্রাদ্ধের সময় দলাদলি পাকায়; বিবাহে যে ঘটকালি করিয়া দেয়, অথচ বউভাতে হয়ত বাঁকিয়া বসে; কাজকর্মে, হাতে-পায়ে ধরিয়া যাহার ক্রোধ শান্তি করিতে হয়, উৎসবে-ব্যসনে যে সাহায্যও করে, বিবাদও করে; যে সহস্র দোষত্রুটি সত্ত্বেও পূজনীয়—আমি তাহাকেই সমাজ বলিতেছি এবং এই সমাজ যদ্দ্বারা শাসিত হয়, সেই বস্তুটিকেই সমাজ-ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিতেছি। তবে, এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, যে ধর্ম নির্বিশেষে সকল দেশের, সকল জাতির সমাজকে শাসন করে, সেই সামাজিক ধর্মের আলোচনা করা আমার প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। কারণ, মানুষ মোটের উপর মানুষই। তাহার সুখ-দুঃখ আচার-ব্যবহারের ধারা সর্বদেশেই একদিকে চলে। মড়া মরিলে সব দেশেই প্রতিবেশীরা সৎকার করিতে জড় হয়; বিবাহে সর্বত্রই আনন্দ করিতে আসে; বাপ-মা সব দেশেই সন্তানের পূজ্য; বয়োবৃদ্ধের সম্মাননা সব দেশেরই নিয়ম; স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ সর্বত্রই প্রায়ই একরূপ; আতিথ্য সর্বদেশেই গৃহস্থের ধর্ম। প্রভেদ শুধু খুঁটিনাটিতে।
মৃতদেহে কেহ-বা গৃহ হইতে গাড়ি-পালকি করিয়া, ফুলের মালায় আবৃত করিয়া গোরস্থানে লইয়া যায়, কেহ-বা ছেঁড়া মাদুরে জড়াইয়া, বংশখণ্ডে বিচালির দড়ি দিয়া বাঁধিয়া, গোবরজলের সৌগন্ধ ছড়াইয়া ঝুলাইতে ঝুলাইতে লইয়া চলে; বিবাহ করিতে কোথাও-বা বরকে তরবারি প্রভৃতি পাঁচ হাতিয়ার বাঁধিয়া যাইতে হয়, আর কোথাও জাঁতিটি হাতে করিয়া গেলেই পাঁচ হাতিয়ারের কাজ হইতেছে মনে করা হয়। বস্ততঃ, এইসব ছোট জিনিস লইয়াই মানুষে মানুষে বাদ-বিতণ্ডা কলহ-বিবাদ। এবং যাহা বড়, প্রশস্ত, সমাজে বাস করিবার পক্ষে যাহা একান্ত প্রয়োজনীয়, সে সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই, হইতেও পারে না। আর পারে না বলিয়াই এখনও ভগবানের রাজ্য বজায় রহিয়াছে; মানুষ সংসারে আজীবন বাস করিয়া জীবনান্তে তাঁহারই পদাশ্রয়ে পৌঁছিবার ভরসা করিতেছে। অতএব মৃতদেহের সৎকার করিতে হয়, বিবাহ করিয়া সন্তান প্রতিপালন করিতে হয়, প্রতিবেশীকে সুবিধা পাইলেই খুন করিতে নাই, চুরি করা পাপ, এইসব স্থূল, অথচ অত্যাবশ্যক সামাজিক ধর্ম সবাই মানিতে বাধ্য; তা তাহার বাড়ি আফ্রিকার সাহারাতেই হউক, আর এশিয়ার সাইবিরিয়াতেই হউক। কিন্তু এই সকল আমার প্রধান আলোচ্য বিষয় নয়। অথচ, এমন কথাও বলি নাই, মনেও করি না যে, যাহা কিছু ছোট, তাহাই তুচ্ছ এবং আলোচনার অযোগ্য। পৃথিবীর যাবতীয় সমাজের সম্পর্কে ইহারা কাজে না আসিলেও বিচ্ছিন্ন এবং বিশেষ সমাজের মধ্যে ইহাদের যথেষ্ট কাজ আছে এবং সে কাজ তুচ্ছ নহে। সকল ক্ষেত্রেই এই সকল কর্মসমষ্টি—যা দেশাচাররূপে প্রকাশ পায়—তাহার যে অর্থ আছে, কিংবা সে অর্থ সুস্পষ্ট, তাহাও নহে; কিন্তু ইহারাই যে বিভিন্ন স্থানে সর্বজনীন সামাজিক ধর্মের বাহক, তাহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। বহন করিবার এই সকল বিচিত্র ধারাগুলিকে চোখ মেলিয়া দেখাই আমার লক্ষ্য।
সামাজিক মানুষকে তিন প্রকার শাসন-পাশ আজীবন বহন করিতে হয়। প্রথম রাজ-শাসন, দ্বিতীয় নৈতিক-শাসন এবং তৃতীয় যাহাকে দেশাচার কহে, তাহারই শাসন।
রাজ-শাসন; আমি স্বেচ্ছাচারী দুর্বৃত্ত রাজার কথা বলিতেছি না—যে রাজা সুসভ্য, প্রজাবৎসল-তাঁহার শাসনের মধ্যে তাঁহার প্রজাবৃন্দেরই সমবেত ইচ্ছা প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তাই খুন করিয়া যখন সেই শাসন-পাশ গলায় বাঁধিয়া ফাঁসিকাঠে গিয়া উঠি, তখন সে ফাঁসের মধ্যে আমার নিজের ইচ্ছা যে প্রকারান্তরে মিশিয়া নাই, একথা বলা যায় না। অথচ মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে আমার নিজের বেলা সেই নিজের ইচ্ছাকে যখন ফাঁকি দিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাই, তখন যে আসিয়া জোর করে, সে-ই রাজশক্তি। শক্তি ব্যতীত শাসন হয় না। এমনি নীতি এবং দেশাচারকে মান্য করিতে যে আমাকে বাধ্য করে, সে-ই আমার সমাজ এবং সামাজিক আইন।
আইনের উদ্ভব সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রচলিত থাকিলেও মুখ্যতঃ রাজার সৃজিত আইন যেমন রাজা-প্রজা উভয়কেই নিয়ন্ত্রিত করে, নীতি ও দেশাচার তেমনি সমাজ-সৃষ্ট হইয়াও সমাজ ও সামাজিক মনুষ্য উভয়কেই নিয়ন্ত্রিত করে।
কিন্তু, এই আইনগুলি কি নির্ভুল? কেহই ত এমন কথা কহে না। ইহার মধ্যে কত অসম্পূর্ণতা, কত অন্যায়, কত অসঙ্গতি ও কঠোরতার শৃঙ্খল রহিয়াছে। নাই কোথায়? রাজার আইনের মধ্যেও আছে, সমাজের আইনের মধ্যেও রহিয়াছে।
এত থাকা সত্ত্বেও, আইন-সম্বন্ধে আলোচনা ও বিচার করিয়া যত লোক যত কথা বলিয়া গিয়াছেন—যদিচ আমি তাঁহাদের মতামত তুলিয়া এই প্রবন্ধের কলেবর ভারাক্রান্ত করিতে চাহি না—মোটের উপর তাঁহারা প্রত্যেকেই স্বীকার করিয়াছেন, আইন যতক্ষণ আইন,—তা ভুলভ্রান্তি তাহাতে যতই কেন থাকুক না, ততক্ষণ—শিরোধার্য তাহাকে করিতেই হইবে। না করার নাম বিদ্রোহ। এবং ”The righteousness of a cause is never alone a sufficient justification of rebellion.”
সামাজিক আইন-কানুন সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে না কি?
আমি আমাদের সমাজের কথাই বলি। রাজার আইন রাজা দেখিবেন, সে আমার বক্তব্য নয়। কিন্তু সামাজিক আইন-কানুনে-ভুলচুক অন্যায়-অসঙ্গতি কি আছে না-আছে, সে না হয় পরে দেখা যাইবে;—কিন্তু এই সকল থাকা সত্ত্বেও ত ইহাকে মানিয়া চলিতে হইবে। যতক্ষণ ইহা সামাজিক শাসন-বিধি, ততক্ষণ ত শুধু নিজের ন্যায্য দাবীর অছিলায় ইহাকে অতিক্রম করিয়া তুমুল কাণ্ড করিয়া তোলা যায় না। সমাজের অন্যায়, অসঙ্গতি, ভুলভ্রান্তি বিচার করিয়া সংশোধন করা যায়, কিন্তু তাহা না করিয়া শুধু নিজের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের বলে একা একা বা দুই চারিজন সঙ্গী লইয়া বিপ্লব বাধাইয়া দিয়া যে সমাজ-সংস্কারের সুফল পাওয়া যায়, তাহা ত কোনমতেই বলা যায় না।
শ্রীযুক্ত রবিবাবুর ‘গোরা’ বইখানি যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন, এই প্রকারের কিছু কিছু আলোচনা তাহাতে আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহার কি মীমাংসা করা হইয়াছে, আমি জানি না। তবে, ন্যায়-পক্ষ হইলে এবং উদ্দেশ্য সাধু হইলে যেন দোষ নেই এই রকম মনে হয়। সত্যপ্রিয় পরেশবাবু সত্যকেই একমাত্র লক্ষ্য করিয়া বিপ্লবের সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। ”সত্য” কথাটি শুনিতে মন্দ নয়, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহার ঠিক চেহারাটি চিনিয়া বাহির করা কঠিন। কারণ, কোন পক্ষই মনে করে না যে, সে অসত্যের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। উভয় পক্ষেরই ধারণা—সত্য তাহারই দিকে।
ইহাতে আরও একটি কথা বলা হইয়াছে যে, সমাজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হাত দিতে পারে না। কারণ, ব্যক্তির স্বাধীনতা সমাজের জন্য সঙ্কুচিত হইতে পারে না। বরঞ্চ, সমাজকেই এই স্বাধীনতার স্থান যোগাইবার জন্য নিজেকে প্রসারিত করিতে হইবে। পণ্ডিত H. Spencer-এর মতও তাই। তবে, তিনি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এই বলিয়া সীমাবদ্ধ করিয়াছেন যে, যতক্ষণ না তাহা অপরের তুল্য স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। কিন্তু, ভাল করিয়া দেখিতে গেলে, এই অপরের তুল্য স্বাধীনতায় যে কার্যক্ষেত্রে কতদিকে কতপ্রকারে টান ধরে, পরিশেষে ঐ ‘সত্য’ কথাটির মত কোথায় যে ‘সত্য’ আছে—তাহার কোন উদ্দেশই পাওয়া যায় না।
যাহা হউক, কথাটা মিথ্যা নয় যে, সামাজিক আইন বা রাজার আইন চিরদিন এমনি করিয়াই প্রসারিত হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু যতক্ষণ তাহা না হইতেছে, ততক্ষণ সমাজ যদি তাহার শাস্ত্র বা অন্যায় দেশাচারে কাহাকেও ক্লেশ দিতেই বাধ্য হয়, তাহার সংশোধন না করা পর্যন্ত এই অন্যায়ের পদতলে নিজের ন্যায্য দাবী বা স্বার্থ বলি দেওয়ায় যে কোন পৌরুষ নাই, তাহাতে যে কোন মঙ্গল হয় না, এমন কথাও ত জোর করিয়া বলা চলে না।
কথাটা শুনিতে হয়ত কতকটা হেঁয়ালির মত হইল। পরে তাহাকে পরিস্ফুট করিতে যত্ন করিব। কিন্তু এইখানে একটা মোটা কথা বলিয়া রাখি যে, রাজশক্তির বিপক্ষে বিদ্রোহ করিয়া তাহার বল ক্ষয় করিয়া তোলায় যেমন দেশের মঙ্গল নাই—একটা ভালর জন্য অনেক ভাল তাহাতে যেমন বিপর্যস্ত, লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়, সমাজ-শক্তির সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই খাটে। এই কথাটা কোনমতেই ভোলা চলে না যে, প্রতিবাদ এক বস্তু, কিন্তু বিদ্রোহ সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। বিদ্রোহকে চরম প্রতিবাদ বলিয়া কৈফিয়ত দেওয়া যায় না। কারণ, ইহা অনেকবার অনেক প্রকারে দেখা গিয়াছে যে, প্রতিষ্ঠিত শাসন-দণ্ডের উচ্ছেদ করিয়া তাহা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ শাসন-দণ্ড প্রবর্তিত করিলেও কোন ফল হয় না, বরঞ্চ কুফলই ফলে।
আমাদের ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলে এই কথাটা অনেকটা বোঝা যায়। সেই সময়ের বাংলা দেশের সহস্র প্রকার অসঙ্গত, অমূলক ও অবোধ্য দেশাচারে বিরক্ত হইয়া কয়েকজন মহৎপ্রাণ মহাত্মা এই অন্যায়রাশির আমূল সংস্কারের তীব্র আকাঙ্ক্ষায়, প্রতিষ্ঠিত সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তিত করিয়া নিজেদের এরূপ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন যে, তাহা নিজেদের যদি বা কাজে লাগিয়া থাকে, দেশের কোন কাজেই লাগিল না। দেশ তাঁহাদের বিদ্রোহী ম্লেচ্ছ খ্রীস্টান মনে করিতে লাগিল। তাঁহারা জাতিভেদ তুলিয়া দিলেন, আহারের আচার-বিচার মানিলেন না, সপ্তাহ অন্তে একদিন গির্জার মত সমাজগৃহে বা মন্দিরের মধ্যে জুতা-মোজা পায়ে দিয়া ভিড় করিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা এত বেশী সংস্কার করিয়া ফেলিলেন যে, তাঁহাদের সমস্ত কার্যকলাপই তৎকাল-প্রতিষ্ঠিত আচার-বিচারের সহিত একেবারে উলটা বলিয়া লোকের চক্ষে পড়িতে লাগিল। ইহা যে হিন্দুর পরম সম্পদ বেদমূলক ধর্ম, সে কথা কেহই বুঝিতে চাহিল না। আজও পাড়াগাঁয়ের লোক ব্রাহ্মদের খ্রীস্টান বলিয়াই মনে করে।
কিন্তু যে-সকল সংস্কার তাঁহারা প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছিলেন, দেশের লোক যদি তাহা নিজেদেরই দেশের জিনিস বলিয়া বুঝিতে পারিত এবং গ্রহণ করিত, তাহা হইলে আজ বাঙালী সমাজের এ দুর্দশা বোধ করি থাকিত না। অসীম দুঃখময় এই বিবাহ-সমস্যা, বিধবার সমস্যা, উন্নতিমূলক বিলাত-যাওয়া-সমস্যা, সমস্তই একসঙ্গে একটা নির্দিষ্ট কূলে আসিয়া পৌঁছিতে পারিত। অন্যপক্ষে গতি এবং বৃদ্ধিই যদি সজীবতার লক্ষণ হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, এই ব্রাহ্ম-সমাজও আজ মৃত্যুমুখে পতিত না হইলেও অকাল-বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছে।
সংস্কার মানেই প্রতিষ্ঠিতের সহিত বিরোধ; এবং অত্যন্ত সংস্কারের চেষ্টাই চরম বিরোধ বা বিদ্রোহ। ব্রাহ্ম-সমাজ এ কথা বিস্মৃত হইয়া অত্যল্পকালের মধ্যেই সংস্কার, রীতি-নীতি, আচার-বিচার সম্বন্ধে নিজেদের এতটাই স্বতন্ত্র এবং উন্নত করিয়া ফেলিলেন যে, হিন্দু-সমাজ হঠাৎ তীব্র ক্রোধ ভুলিয়া হাসিয়া ফেলিল এবং নিজেদের অবসরকালে ইহাদিগকে লইয়া এখানে ওখানে বেশ একটু আমোদ করিতেও লাগিল।
হায় রে! এমন ধর্ম, এমন সমাজ, পরিশেষে কিনা পরিহাসের বস্তু হইয়া উঠিল! জানি না, এই পরিহাসের জরিমানা কোনদিন হিন্দুকে সুদ-সুদ্ধ উসুল দিতে হইবে কি না। কিন্তু ব্রাহ্মই বল, আর হিন্দুই বল, বাংলার বাঙালী-সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল দুই দিক দিয়াই।
আরও একটা কথা এই যে, সামাজিক আইন-কানুন প্রতিষ্ঠিত হয় যে দিক দিয়া, তাহার সংস্কারও হওয়া চাই সেই দিক দিয়া; শাসন-দণ্ড পরিচালন করেন যাঁহারা, সংস্কার করিবেন তাঁহারাই। অর্থাৎ, মনু-পরাশরের বিধিনিষেধ মনু-পরাশরের দিক দিয়াই সংস্কৃত হওয়া চাই। বাইবেল কোরান হাজার ভাল হইলেও কোন কাজেই আসিবে না। দেশের ব্রাহ্মণেরাই যদি সমাজ-যন্ত্র এতাবৎকাল পরিচালন করিয়া আসিয়া থাকেন, ইহার মেরামতি-কার্য তাঁহাদিগকে দিয়াই করাইয়া লইতে হইবে। এখানে হাইকোর্টের জজেরা হাজার বিচক্ষণ হওয়া সত্ত্বেও কোন সাহায্যই করিতে পারিবেন না। দেশের লোক এ-বিষয়ে পুরুষানুক্রমে যাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে অভ্যাস করিয়াছে—হাজার বদ অভ্যাস হইলেও সে অভ্যাস তাহারা ছাড়িতে চাহিবে না!
এ-সকল স্থূল সত্য কথা। সুতরাং আশা করি, এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি, সে সম্বন্ধে বিশেষ কাহারো মতভেদ হইবে না।
যদি না হয়, তবে একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, মনু-পরাশরের হাত দিয়াই যদি হিন্দুর অবনতি পৌঁছিয়া থাকে ত উন্নতিও তাঁহাদের হাত দিয়াই পাইতে হইবে—অন্য কোন জাতির সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা, তা সে যত উন্নতই হউক, হিন্দুকে কিছুই দিতে পারিবে না। তুলনায় সমালোচনায় দোষগুণ কিছু দেখাইয়া দিতে আরে, এইমাত্র।
কিন্তু যে-কোন বিধি-ব্যবস্থা হউক, যাহা মানুষকে শাসন করে, তাহার দোষগুণ কি দিয়া বিচার করা যায়? তাহার সুখ-সৌভাগ্য দিবার ক্ষমতা দিয়া, কিংবা তাহার বিপদ ও দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা দিয়া? Sir William Markly তাঁহার Elements of Law গ্রন্থে বলেন—“The value is to be measured not by the happiness which it procures, but by the misery from which it preserves us.” আমিও ইহাই বিশ্বাস করি। সুতরাং মনু-পরাশরের বিধি-ব্যবস্থা আমাদের কি সম্পদ দান করিয়াছে, সে তর্ক তুলিয়া নয়, কি বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, শুধু সেই আলোচনা করিয়া সমাজের দোষগুণ বিচার করা উচিত। অতএব, আজও যদি আমাদের ঐ মনু-পরাশরের সংস্কার করাই আবশ্যক হইয়া থাকে, তবে ঐ ধারা ধরিয়াই করা চাই।
স্বর্গই হউক আর মোক্ষই হউক, সে কি দিতেছে, সে বিচার করিয়া নয়, বরঞ্চ সব বিপদ হইতে আজ আর সে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিতেছে না, শুধু সেই বিচার করিয়া। সুতরাং, হিন্দু যখন উপর দিকে চাহিয়া বলেন, ঐ দেখ আমাদের ধর্মশাস্ত্র স্বর্গের কবাট সোজা খুলিয়া দিয়াছেন, আমি তখন বলি—সেটা না হয় পরে দেখিয়ো, কিন্তু আপাততঃ নীচের দিকে চাহিয়া দেখ, নরকে পড়িবার দুয়ারটা সম্প্রতি বন্ধ করা হইয়াছে কি না। কারণ, এটা ওটার চেয়েও আবশ্যক। সহস্র বর্ষ পূর্বে হিন্দুশাস্ত্র স্বর্গপ্রবেশের যে সোজা পথটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সে পথটি আজও নিশ্চয় তেমনই আছে। সেখানে পৌঁছিয়া একদিন সেইরূপ আমোদ উপভোগ করিবার আশা বেশী কথা নয়—কিন্তু, নানাপ্রকার বিজাতীয় সভ্যতা অসভ্যতার সংঘর্ষে ইতিমধ্যে নীচে পড়িয়া পিষিয়া মরিবার যে নিত্য নূতন পথ খুলিয়া যাইতেছে, সেগুলি ঠেকাইবার কোনরূপ বিধি-ব্যবস্থা শাস্ত্রগ্রন্থে আছে কি না, সম্প্রতি তাহাই খুঁজিয়া দেখ। যদি না থাকে, প্রস্তুত কর; তাহাতেও দোষ নাই; বিপদে রক্ষা করাই ত আইনের কাজ। কিন্তু উদ্দেশ্য ও আবশ্যক যত বড় হউক, ‘প্রস্তুত’ শব্দটা শুনিবামাত্রই হয়ত পণ্ডিতদের দল চেঁচাইয়া উঠিবেন। আরে এ বলে কি! এ কি যার-তার শাস্ত্র যে, আবশ্যকমত দুটো কথা বানাইয়া লইব? এ যে হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থ! অপৌরুষেয়—অন্ততঃ ঋষিদের তৈরি, যাঁরা ভগবানের কৃপায় ভূত-ভবিষ্যৎ সমস্ত জানিয়া শুনিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ কথা তাঁরা স্মরণ করেন না যে, এটা শুধু হিন্দুর উপরেই ভগবানের দয়া নয়—এমনি দয়া সব জাতির প্রতিই তিনি করিয়া গিয়াছেন। ইহুদিরাও বলে তাই, খ্রীস্টান, মুসলমান—তারাও তাই বলে। কেহই বলে না যে, তাহাদের ধর্ম এবং শাস্ত্রগ্রন্থ, সাধারণ মানুষের সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনার ফল। এ বিষয়ে হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থের বিশেষ কোন একটা বিশেষত্ব আমি ত দেখিতে পাই না। সকলেরই যেমন করিয়া পাওয়া, আমাদেরও তেমনি করিয়া পাওয়া। সে যাই হউক, আবশ্যক হইলে শাস্ত্রীয় শ্লোক একটা বদলাইয়া যদি আর একটা নাও করা যায়—নতুন একটা রচনা করিয়া বেশ দেওয়া যায়। এবং এমন কাণ্ড বহুবার হইয়াও গিয়াছে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। আর তাই যদি না হইবে, তবে যে-কোন একটা বিধি-নিষিধের এত প্রকার অর্থ, এত প্রকার তাৎপর্য পাওয়া যায় কেন?
এই “ভারতবর্ষ’’ কাগজেই অনেকদিন পূর্বে ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশবাবু বলিয়াছিলেন, “না জানিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়ো না!” কিন্তু, আমি ত বলি, সেই একমাত্র কাজ, যাহা শাস্ত্র না জানিয়া পারা যায়। কারণ, জানিলে তাহার আর শাস্ত্রের দোহাই পাড়িবার কিছুমাত্র জো থাকে না। তখন ‘বাঁশবনে ডোম কানা’ হওয়ার মত সে ত নিজেই কোনদিকে কূল-কিনারা খুঁজিয়া পায় না; সুতরাং, কথায় কথায় সে শাস্ত্রের দোহাই দিতেও যেমন পারে না, মতের অনৈক্য হইলেই বচনের মুগুর হাতে করিয়া তাড়িয়া মারিতে যাইতেও তাহার তেমনি লজ্জা করে।
এই কাজটা তাহারাই ভাল পারে, যাহাদের শাস্ত্রজ্ঞানের পুঁজি যৎসামান্য। এবং ঐ জোরে তাহারা অমন নিঃসঙ্কোচে শাস্ত্রের দোহাই মানিয়া নিজের মত গায়ের জোরে জাহির করে এবং নিজেদের বিদ্যার বাহিরে সমস্ত আচার-ব্যবহারই অশাস্ত্রীয় বলিয়া নিন্দা করে।
কিন্তু মানবের মনের গতি বিচিত্র। তাহার আশা–আকাঙ্ক্ষা অসংখ্য। তাহার সুখ–দুঃখের ধারণা বহুপ্রকার। কালের পরিবর্তন ও উন্নতি অবনতির তালে তালে সমাজের মধ্যে সে নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি করে। চিরদিন করিয়াছে এবং চিরদিনই করিবে। ইহার মধ্যে সমাজ যদি নিজেকে অদম্য অপরিবর্তনীয় কল্পনা করিয়া, ঋষিদের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির উপর বরাত দিয়া, নির্ভয়ে পাথরের মত কঠিন হইয়া থাকিবার সঙ্কল্প করে ত তাহাকে মরিতেই হইবে। এই নির্বুদ্ধিতার দোষে অনেক বিশিষ্ট সমাজও পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ দুর্ঘটনা বিরল নয়; কিন্তু, আমাদের এই সমাজ, মুখে সে যাই বলুক, কিন্তু কাজে যে সত্যিই মুনিঋষির ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া তাহার শাস্ত্র জিনিসটিকে লোহার শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখে নাই, তাহার সকলের চেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, সে সমাজ এখনও টিকিয়া আছে। বাহিরের সহিত ভিতরের সামঞ্জস্য রক্ষা করাই ত বাঁচিয়া থাকা। সুতরাং সে যখন বাঁচিয়া আছে, তখন যে–কোন উপায়ে, যে–কোন কলাকৌশলের দ্বারা সে যে এই সামঞ্জস্য করিয়া আসিয়াছে, তাহা ত স্বতঃসিদ্ধ।
সর্বত্রই সমস্ত বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই সামঞ্জস্য প্রধানতঃ যে উপায়ে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে—তাহা প্রকাশ্যে নূতন শ্লোক রচনা করিয়া নহে। কারণ, দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় জানা গিয়াছে যে, নব–রচিত শ্লোক বেনামীতে এবং প্রাচীনতার ছাপ লাগাইয়া চালাইয়া দিতে পারিলেই তবে ছুটিয়া চলে, না হইলে খোঁড়াইতে থাকে। অতএব, নিজের জোরে নূতন শ্লোক তৈরি করা প্রকৃষ্ট উপায় নহে। প্রকৃষ্ট উপায় ব্যাখ্যা।
তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—পুরাতন সভ্য–সমাজের মধ্যে শুধু গ্রীক ও রোম ছাড়া আর সকল জাতি এই দাবী করিয়াছে,—তাহাদের শাস্ত্র ঈশ্বরের দান। অথচ, সকলকেই নিজেদের বর্ধনশীল সমাজের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য এই ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্রের পরিসর ক্রমাগত বাড়াইয়া তুলিতে হইয়াছে। এবং সে–বিষয়ে সকলেই প্রায় এক পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন বর্তমান শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া।
কোন জিনিসের ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করা যায় তিন প্রকারে। প্রথম—ব্যাকরণগত ধাতুপ্রত্যয়ের জোরে; দ্বিতীয়— পূর্বে এবং পরবর্তী শ্লোকের সহিত তাহার সম্বন্ধ বিচার করিয়া; এবং তৃতীয়—কোন বিশেষ দুঃখ দূর করিবার অভিপ্রায়ে শ্লোকটি সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় করিয়া। অর্থাৎ চেষ্টা করিলেই দেখা যায় যে, চিরদিন সমাজ–পরিচালকেরা নিজেদের হাতে এই তিনখানি হাতিয়ার—ব্যাকরণ, সম্বন্ধ এবং তাৎপর্য (positive and negative) লইয়া ঈশ্বরদত্ত যে–কোন শাস্ত্রীয় শ্লোকের যে–কোন অর্থ করিয়া পরবর্তী যুগের নিত্য নূতন সামাজিক প্রয়োজন ও তাহার ঋণ পরিশোধ করিয়া তাহাকে সজীব রাখিয়া আসিয়াছেন।
আজ যদি আমাদের জাতীয় ইতিহাস থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয় দেখিতে পাইতাম—কেন শাস্ত্রীয় বিধি–ব্যবস্থা এমন করিয়া পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে এবং কেনই বা এত মুনির এত রকম মত প্রচলিত হইয়াছে এবং কেনই বা প্রক্ষিপ্ত শ্লোকে শাস্ত্র বোঝাই হইয়া গিয়াছে। সমাজের এই ধারাবাহিক ইতিহাস নাই বলিয়াই এখন আমরা ধরিতে পারি না—অমুক শাস্ত্রের অমুক বিধি কিজন্য প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং কিজন্যই বা অমুক শাস্ত্রের দ্বারা তাহাই বাধিত হইয়াছিল। আজ সুদূরে দাঁড়াইয়া সবগুলি আমাদের চোখে এইরূপ দেখায়। কিন্তু, যদি তাহাদের নিকটে যাইয়া দেখিবার কোন পথ থাকিত ত নিশ্চয় দেখিতে পাইতাম—এই দুটি পরস্পর–বিরুদ্ধ বিধি একই স্থানে দাঁড়াইয়া আঁচড়া–আঁচড়ি করিতেছে না। একটি হয়ত আর–একটির শতবর্ষ পিছনে দাঁড়াইয়া ঠোঁটে আঙুল দিয়া নিঃশব্দে হাসিতেছে।
প্রবাহই জীবন। মানুষ যতক্ষণ বাঁচিয়া থাকে, ততক্ষণ একটা ধারা তাহার ভিতর দিয়া অনুক্ষণ বহিয়া যাইতে থাকে। বাহিরের প্রয়োজনীয়–অপ্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তুকে সে গ্রহণও করে, আবার ত্যাগও করে। যাহাতে তাহার আবশ্যক নাই, যে বস্তু দূষিত, তাহাকে পরিবর্জন করাই তাহার প্রাণের ধর্ম। কিন্তু মরিলে আর যখন ত্যাগ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না, তখনই তাহাতে বাহির হইতে যাহা আসে, তাহারা কায়েম হইয়া বসিয়া যায় এবং মৃতদেহটাকে পচাইয়া তোলে। জীবন্ত সমাজ এ নিয়ম স্বভাবতই জানে। সে জানে, যে বস্তু আর তাহার কাজে লাগিতেছে না, মমতা করিয়া তাহাকে ঘরে রাখিলে মরিতেই হইবে। সে জানে, আবর্জনার মত তাহাকে ঝাঁটাইয়া না ফেলিয়া দিয়া, অনর্থক ভার বহিয়া বেড়াইলে অনর্থক শক্তিক্ষয় হইতে থাকিবে, এবং এই ক্ষয়ই একদিন তাহাকে মৃত্যুর মুখে ডালিয়া দিবে।
কিন্তু জীবনীশক্তি যত হ্রাস পাইতে থাকে, প্রবাহ যতই মন্দ হইতে মন্দতর হইয়া আসিতে থাকে, যতই তাহার দুর্বলতা দুষ্টের ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দিতে ভয় পায়, ততই তাহার ঘরে প্রয়োজনীয়–অপ্রয়োজনীয় ভাল– মন্দের বোঝা জমাট বাঁধিয়া উঠিতে থাকে। এবং সেই সমস্ত গুরুভার মাথায় লইয়া সেই জরাতুর মরণোন্মুখ সমাজকে কোনমতে লাঠিতে ভর দিয়া ধীরে ধীরে সেই শেষ আশ্রয় যমের বাড়ির পথেই যাইতে হয়।
ইহার কাছে এখন সমস্তই সমান—ভালও যা, মন্দও তাই; সাদাও যেমন, কালও তেমনই। কারণ জানিলে তবেই কাজ করা যায়, অবস্থার সহিত পরিচয় থাকিলেই তবে ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। এখানকার এই জরাতুর সমাজ জানেই না—কিজন্য বিধি প্রবর্তিত হইয়াছিল, কেনই বা তাহা প্রকারান্তরে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। মানুষের কোন্ দুঃখ সে দূর করিতে চাহিয়াছিল, কিংবা কোন্ পাপের আক্রমণ হইতে সে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এই অর্গল টানিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল। নিজের বিচার–শক্তি ইহার নাই, পরের কাছেও যে সমস্ত গন্ধমাদন তুলিয়া লইয়া হাজির করিবে—সে জোরও ইহার গিয়াছে। সুতরাং, এখন এ শুধু এই বলিয়া তর্ক করে যে, এই–সকল শাস্ত্রীয় বিধি– নিষেধ আমাদেরই ভগবান ও পরমপূজ্য মুনিঋষির তৈরি।
এই তপোবনেই তাঁরা মৃতসঞ্জীবনী লতাটি পুঁতিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং, যদিচ প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ও নিরর্থক ব্যাখ্যারূপ গুল্ম ও কণ্টকতৃণে এই তপোবনের মাঠটি সম্প্রতি সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই পরম শ্রেয়ঃ ইহারই মধ্যে কোথাও প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেই। অতএব আইস, হে সনাতন হিন্দুর দল, আমরা এই হোম–ধূম–পূত মাঠের সমস্ত ঘাস ও তৃণ চক্ষু মুদিয়া নির্বিকারে চর্বণ করিতে থাকি। আমরা অমৃতের পুত্র—সুতরাং সেই অমৃত–লতাটি একদিন যে আমাদের দীর্ঘ জিহ্বায় আটক খাইবেই, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।
ইহাতে সংশয় না থাকিতে পারে। কিন্তু অমৃতের সকল সন্তানই কাঁচা ঘাস হজম করিতে পারিবে কি না, তাহাতেও কি সংশয় নাই!
কিন্তু আমি বলি, এই উদর এবং জিহ্বার উপর নির্ভর না করিয়া বুদ্ধি এবং দৃষ্টিশক্তির সাহায্য লইয়া কাঁটাগাছগুলা বাছিয়া ফেলিয়া, সেই অমৃত–লতাটির সন্ধান করিলে কি কাজটা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং মানুষের মত দেখিতে হয় না?
ভগবান মানুষকে বুদ্ধি দিয়াছেন কিজন্য? সে কি শুধু আর একজনের লেখা শাস্ত্রীয় শ্লোক মুখস্থ করিবার জন্য? এবং একজন তাহার কি টীকা করিয়াছেন, এবং আর একজন সে টীকার কি অর্থ করিয়াছেন—তাহাই বুঝিবার জন্য? বুদ্ধির আর কি কোন স্বাধীন কাজ নাই? কিন্তু বুদ্ধির কথা তুলিলেই পণ্ডিতেরা লাফাইয়া উঠেন; ক্রুদ্ধ হইয়া বারংবার চীৎকার করিতে থাকেন। শাস্ত্রের মধ্যে বুদ্ধি খাটাইবে কোন্খানে? এ যে শাস্ত্র! তাঁদের বিশ্বাস, শাস্ত্রীয় বিচার শুধু শাস্ত্রকথার লড়াই। তাহার হেতু, কারণ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সত্য, মিথ্যা, এ–সকল নিরূপণ করা নয়। শাস্ত্র– ব্যবসায়ীরা কতকাল হইতে যে এরূপ অবনত হীন হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা জানিবার উপায় নাই —কিন্তু এখন তাঁহাদের একমাত্র ধারণা যে, ব্রহ্মপুরাণের কুস্তির প্যাঁচ বায়ুপুরাণ দিয়া খসাইতে হইবে। আর পরাশরের লাঠির মার হারীতের লাঠিতে ঠেকাইতে হইবে। আর কোন পথ নাই। সুতরাং, যে ব্যক্তি এই কাজটা যত ভাল পারেন, তিনি তত বড় পণ্ডিত। ইহার মধ্যে শিক্ষিত ভদ্রব্যক্তির স্বাভাবিক সহজ বুদ্ধির কোন স্থানই নাই। কারণ, সে শ্লোক ও ভাষ্য মুখস্থ করে নাই।
অতএব, হে শিক্ষিত ভদ্রব্যক্তি! তুমি শুধু তোমাদের সমাজের নিরপেক্ষ দর্শকের মত মিটমিট করিয়া চাহিয়া থাক, এবং শাস্ত্রীয় বিচারের আসরে স্মৃতিরত্ন আর তর্করত্ন কণ্ঠস্থ শ্লোকের গদ্কা ভাঁজিয়া যখন আসর গরম করিয়া তুলিবেন, তখন হাততালি দাও।
কিন্তু তামাশা এই যে, জিজ্ঞাসা করিলে এইসব পণ্ডিতেরা বলিতেও পারিবেন না—কেন তাঁরা ও– রকম উন্মত্তের মত ওই যন্ত্রটা ঘুরাইয়া ফিরিতেছেন! এবং কি তাঁদের উদ্দেশ্য! কেনই বা এই আচারটা ভাল বলিতেছেন এবং কেনই বা এটার বিরুদ্ধে এমন বাঁকিয়া বসিতেছেন। যদি প্রশ্ন করা যায়, তখনকার দিনে যে উদ্দেশ্য বা যে দুঃখের নিষ্কৃতি দেবার জন্য অমুক বিধি–নিষেধ প্রবর্তিত হইয়াছিল—এখনও কি তাই আছে; ইহাতেই কি মঙ্গল হইবে? প্রত্যুত্তরে স্মৃতিরত্ন তাঁহার গদ্কা বাহির করিয়া তোমার সম্মুখে ঘুরাইতে থাকিবেন, যতক্ষণ না তুমি ভীত ও হতাশ হইয়া চলিয়া যাও।
এইখানে আমি একটি প্রবন্ধের বিস্তৃত সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করি। কারণ, তাহাতে আপনা হইতেই অনেক কথা পরিস্ফুট হইবার সম্ভাবনা। প্রবন্ধটি অধ্যাপক শ্রীভববিভূতি ভট্টাচার্য বিদ্যাভূষণ এম. এ. লিখিত ‘ঋগ্বেদে চাতুর্ব্বণ্য ও আচার’ মাঘের ‘ভারতবর্ষে’ প্রথমেই ছাপা হইয়া বোধ করি, ইহা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।
কিন্তু আমি আকৃষ্ট হইয়াছি, ইহার শাস্ত্রীয় বিচারের সনাতন পদ্ধতিতে, ইহার ঝাঁজে এবং রৌদ্র, করুণ প্রভৃতি রসের উত্তাপে এবং উচ্ছ্বাসে।
প্রবন্ধটি পড়িয়া আমার স্বর্গীয় মহাত্মা রামমোহন রায়ের সেই কথাটি মনে পড়িয়া গিয়াছিল। শাস্ত্রীয় বিচারে যিনি মাথা গরম করেন, তিনি দুর্বল। এইজন্য একবার মনে করিয়াছিলাম, এই প্রবন্ধের সমালোচনা না করাই উচিত। কিন্তু ঠিক এই ধরনের আর কোন প্রবন্ধ হাতের কাছে না পাওয়ায় শেষে বাধ্য হইয়া ইহারই আলোচনাকে ভূমিকা করিতে হইল। কারণ, আমি যাহার মূল্য–নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহারই কতকটা আভাস এই ‘চাতুর্ব্বণ্য’ প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে।
এই প্রবন্ধে ভববিভূতি মহাশয় স্বর্গীয় রমেশ দত্তের উপর ভারী খাপ্পা হইয়াছেন। প্রথম কারণ, তিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পদাঙ্কানুসারী দেশীয় বিদ্বানগণের অন্যতম। এই পাপে তাঁর টাইটেল দেওয়া হইয়াছে ‘পদাঙ্কানুসারী রমেশ দত্ত’—যেমন মহামহোপাধ্যায় অমুক, রায় বাহাদুর অমুক, এই প্রকার। যেখানেই স্বর্গীয় দত্ত মহাশয় উল্লিখিত হইয়াছেন, সেইখানেই এই টাইটেলটি বাদ যায় নাই। দ্বিতীয় এবং ক্রোধের মুখ্য কারণ বোধ করি এই, ‘পূজ্যপাদ পিতৃদেব শ্রীহৃষিকেশ শাস্ত্রী মহাশয়’ তাঁহার শুদ্ধিতত্ত্বের ৪৫ পৃষ্ঠায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীকাশীরাম বাচস্পতির টীকার নকল করিয়া ‘অগ্নে’ লেখা সত্ত্বেও এই পদাঙ্কানুসারী বঙ্গীয় অনুবাদকটা ‘অগ্রে’ লিখিয়াছে! শুধু তাই নয়। আবার ‘অগ্নে’ শব্দটাকে প্রক্ষিপ্ত পর্যন্ত মনে করিয়াছে! সুতরাং এই অধ্যাপক ভট্টাচার্য মহাশয়ের নানাপ্রকার রসের উৎসব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। যথা—“স্তম্ভিত হইবেন, লজ্জায় ঘৃণায় অধোবদন হইবেন এবং যদি একবিন্দুও আর্যরক্ত আপনাদের ধমনীতে প্রবাহিত হয়, তবে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিবেন” ইত্যাদি ইত্যাদি। সব উচ্ছ্বাসগুলি লিখিতে গেলে সে অনেক স্থান এবং সময়ের আবশ্যক। সুতরাং তাহাতে কাজ নাই; যাঁহার অভিরুচি হয়, তিনি ভট্টাচার্য মহাশয়ের মূল প্রবন্ধে দেখিয়া লইবেন। তথাপি এ-সকল কথা আমি তুলিতাম না। কিন্তু এই দুটা কথা আমি সুস্পষ্ট করিয়া দেখাইতে চাই, আমাদের দেশের শাস্ত্রীর বিচার এবং শাস্ত্রীয় আলোচনা কিরূপ ব্যক্তিগত ও নিরর্থক উচ্ছ্বাসপূর্ণ হইয়া উঠে। এবং উৎকট গোঁড়ামি ধমনীর আর্যরক্তে এমন করিয়া তাণ্ডব নৃত্য বাধাইয়া দিলে মুখ দিয়া শুধু যে মান্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপভাষাই বাহির হয়, তাহা নয়, এমন সব যুক্তি বাহির হয়, যাহা শাস্ত্রীয় বিচারেই বল, আর যে-কোন বিচারেই বল, কোন কাজেই লাগে না। কিন্তু স্বর্গীয় দত্ত মহাশয়ের অপরাধটা কি? পণ্ডিতের পদাঙ্ক ত পণ্ডিতেই অনুসরণ করিয়া থাকে। সে কি মারাত্মক অপরাধ? পাশ্চাত্য পণ্ডিত কি পণ্ডিত নন যে, তাঁহার মতানুযায়ী হইলেই গালিগালাজ খাইতে হইবে!
দ্বিতীয় বিবাদ ঋক্বেদের ‘অগ্নে’ শব্দ লইয়া। এই পদাঙ্কানুসারী লোকটা কেন যে জানিয়া শুনিয়াও এ শব্দটাকে প্রক্ষিপ্ত মনে করিয়া ‘অগ্রে’ পাঠ গ্রহণ করিয়াছিল, সে আলোচনা পরে হইবে। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কি জানা নাই যে, বাংলার অনেক পণ্ডিত আছেন যাঁহারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতের পদাঙ্ক অনুসরণ না করিয়াও অনেক প্রামাণ্য শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, এবং তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কারণ, বুদ্ধিপূর্বক নিরপেক্ষ আলোচনার দ্বারা যদি কোন শাস্ত্রীয় শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়, তাহা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া বলাই ত শাস্ত্রের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা।
জ্ঞানতঃ চাপাচুপি দিয়া রাখা বা অজ্ঞানতঃ প্রত্যেক অনুস্বার বিসর্গটিকে পর্যন্ত নির্বিচারে সত্য বলিয়া প্রচার করায় কোন পৌরুষ নাই। তাহাতে শাস্ত্রেরও মান্য বাড়ে না, ধর্মকেও খাটো করা হয়। বরঞ্চ, যাহাদের শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাসের দৃঢ়তা নাই, শুধু তাহাদেরই এই ভয় হয়, পাছে দুই-একটা কথাও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরা পড়িলে সমস্ত বস্তুটাই ঝুটা হইয়া ছায়াবাজির মত মিলাইয়া যায়। সুতরাং যাহা কিছু সংস্কৃত শ্লোকের আকারে ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার সমস্তটাই হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া মানা চাই-ই।
বস্তুতঃ, এই সত্য ও স্বাধীন বিচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই হিন্দুর শাস্ত্ররাশি এমন অধঃপাতিত হইয়াছে। নিছক নিজের বা দলটির সুবিধার জন্য কত যে রাশি রাশি মিথ্যা উপন্যাস রচিত এবং অনুপ্রবিষ্ট হইয়া হিন্দুর শাস্ত্র ও সমাজকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে, কত অসত্য যে বেনামীতে প্রাচীনতার ছাপ মাখিয়া ভগবানের অনুশাসন বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহার সীমা-পরিসীমা নাই। জিজ্ঞাসা করি, ইহাকে মান্য করাও কি হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা করা? একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বলি। কুলার্ণবের “আমিষাসবসৌরভ্যহীনং যস্য মুখং ভবেৎ। প্রায়শ্চিত্তী স বর্জ্জ্যাশ্চ পশুরেব ন সংশয়ঃ” ইহাও হিন্দুর শাস্ত্র! এ কথাও ভগবান মহাদেব বলিয়া দিয়াছেন! চব্বিশ ঘণ্টা মুখে মদ-মাংসের সুগন্ধ না থাকিলে সে একটা অন্ত্যজ জানোয়ারের সামিল। অধিকারিভেদে এই শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের দ্বারাও হিন্দু স্বর্গের আশা করে! কিন্তু তান্ত্রিকই হউক, আর যাই হউক, সে হিন্দু ত বটে! ইহা শাস্ত্রীয় বিধি ত বটে! সুতরাং স্বর্গবাসও ত সুনিশ্চিত বটে! কিন্তু, তবুও যদি কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত humbug বলিয়া হাসিয়া উঠেন, তাঁহার হাসি থামাইবারও ত কোন সদুপায় দেখিতে পাওয়া যায় না।
অথচ হিন্দুর ঘরে জন্মিয়া শ্লোকটিকে মিথ্যা বলাতেও শঙ্কা আছে। কারণ, আর দশটা হিন্দু-শাস্ত্র হইতে বচন বাহির হইয়া পড়িবে যে, মহেশ্বরের তৈরি এই শ্লোকটিকে যদি কেহ সন্দেহ করে, তাহা হইলে সে ত সে, তাহার ৫৬ পুরুষ নরকে যাইবে। আমাদের হিন্দুশাস্ত্র ত সচরাচর একপুরুষ লইয়া বড়-একটা কথা কহে না।
শ্রীভববিভূতি ভট্টাচার্য এম. এ. মহোদয় তাঁহার ‘চাতুর্ব্বণ্য ও আচার’ প্রবন্ধের গোড়াতেই চাতুর্ব্বণ্য সম্বন্ধে বলিতেছেন,—“যে চাতুর্ব্বণ্য প্রথা হিন্দু জাতির একটি মহৎ বিশেষত্ব, যাহা পৃথিবীর অন্য কোনও জাতিতে দৃষ্ট হয় না—যে সনাতন সুপ্রথা শান্তি ও সুশৃঙ্খলার সহিত সমাজ পরিচালনার একমাত্র সুন্দর উপায়,—যাহাকে কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও তাঁহাদের পদাঙ্কানুসারী দেশীয় বিদ্বান্গণ হিন্দুর প্রধান ভ্রম এবং তাঁহাদের অধঃপতনের মূল কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন,—সেই চাতুর্ব্বর্ণ্য কত প্রাচীন, তাহা জানিতে হইলে বেদপাঠ তাহার অন্যতম সহায়।”
এই চাতুর্ব্বণ্য প্রসঙ্গে শুধু যদি ইনি লিখিতেন—এই কথা কত প্রাচীন, তাহা জানিতে হইলে বেদপাঠ তাহার অন্যতম সহায়, তাহা হইলে কোন কথা ছিল না; কারণ, উক্ত প্রবন্ধে বলিবার বিষয়ই এই। কিন্তু ঐ যে-সব আনুষঙ্গিক বক্র কটাক্ষ, তাহার সার্থকতা কোনখানে? “যে সনাতন সুপ্রথা শান্তি ও সমাজ-পরিচালনার একমাত্র সুন্দর উপায়—” জিজ্ঞাসা করি, কেন? কে বলিয়াছে? ইহা যে ‘সুপ্রথা’ তাহার প্রমাণ কোথায়? যে-কোন একটা প্রথা শুধু পুরাতন হইলেই ‘সু’ হয় না। ফিজিয়ানরা যদি জবাব দেয়, “মশাই, বুড়া বাপ-মাকে জ্যান্ত পুঁতিয়া ফ্যালার নিয়ম যে আমাদের দেশের কত প্রাচীন, সে যদি একবার জানিতে ত আর আমাদের দোষ দিতে না।”
সুতরাং এই যুক্তিতে ত ঘাড় হেঁট করিয়া আমাদিগকে বলিতে হইবে, “হাঁ বাপু, তোমার কথাটা সঙ্গত বটে! এ-প্রথা যখন এতই প্রাচীন, তখন আর ত কোন দোষ নাই। তোমাকে নিষেধ করিয়া অন্যায় করিয়াছি—বেশ করিয়া জ্যান্ত কবর দাও—এমন সুবন্দোবস্ত আর হইতেই পারে না!” অতএব শুধু প্রাচীনত্বই কোন বস্তুর ভাল-মন্দর সাফাই নয়। তবে এই যে বলা হইয়াছে যে, এই প্রথা কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রবর্তিত নহে, ইহা সেই পরমপুরুষের একটি ‘অঙ্গবিলাস’ মাত্র, তাহা হইলে আর কথা চলে না। কিন্তু আমার কথা চলুক আর না-চলুক, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না; কিন্তু যাহাতে যথার্থই আসিয়া যায়, অন্ততঃ আসিয়া গিয়াছে, তাহা এই যে, সেই সমস্ত প্রাচীন দিনের ঋষিদিগের অপরিমেয় অতুল্য বুদ্ধিরাশির ভরা-নৌকা এইখানেই ঘা খাইয়া চিরদিনের মত ডুবিয়াছে। যে-কেহ হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন, তিনিই বোধ করি অত্যন্ত ব্যথার সহিত অনুভব করিয়াছেন, কি করিয়া ঋষিদিগের স্বাধীন চিন্তার শৃঙ্খল এই বেদেরই তীক্ষ্ণ খড়্গে ছিন্নভিন্ন হইয়া পথে-বিপথে যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন করিয়া আজ পড়িয়া আছে। চোখ মেলিলেই দেখা যায়, যখনই সেই সমস্ত বিপুল চিন্তার ধারা সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া ছুটিতে গিয়াছে, তখনই বেদ তাহার দুই হাত বাড়াইয়া তাহাদের চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া আর একদিকে ফিরাইয়া দিয়াছে। তাহাদিগকে ফিরাইয়াছে সত্য, কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিত বা তাঁহাদেরই পদাঙ্কানুসারী দেশীয় বিদ্বান্গণকে ঠিক তেমন করিয়া নিবৃত্ত করা শক্ত।
কিন্তু সে যাই হউক, কেন যে তাঁহারা এই প্রথমটিকে হিন্দুর ভ্রম এবং অধঃপতনের হেতু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, অধ্যাপক মহাশয় তাহার যখন কিছুমাত্র হেতুর উল্লেখ না করিয়া শুধু উক্তিটা তুলিয়া দিয়াই ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন ইহা লইয়া আলোচনা করিবার আপাততঃ প্রয়োজন অনুভব করি না।
অতঃপর অধ্যাপক মহাশয় বলেন বৈদেশিক পণ্ডিতেরা পরমপুরুষের এই চাতুর্ব্বণ্য অঙ্গবিলাসটি মানিতে চাহেন না এবং বলেন, ঋক্বেদের সময়ে চাতুর্বর্ণ্য ছিল না। কারণ, এই বেদের আদ্য কতিপয় মণ্ডলে ভারতবাসিগণের কেবল দ্বিবিধ ভেদের উল্লেখ আছে। আর যদিই বা কোনস্থানে চাতুর্বর্ণ্যের উল্লেখ থাকে, তবে তাহা প্রক্ষিপ্ত।
এই কথায় অধ্যাপক মহাশয় ইহাদিগকে অন্ধ বলিয়া ক্রোধে ইহাদের চোখে আঙুল দিয়া দিবেন বলিয়া শাসাইয়াছেন। কারণ, আর্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চতুর্বিধ ভেদের স্পষ্ট উল্লেখ থাকিতেও তাহা তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।
তার পর ‘আর্য্যং বর্ণং’ শব্দটার অর্থ লইয়া উভয় পক্ষের যৎকিঞ্চিৎ বচসা আছে। কিন্তু আমরা ত বেদ জানি না, সুতরাং এই ‘আর্য্যং বর্ণং’ শেষে কি মানে হইল, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।
তবে মোটামুটি বুঝা গেল যে, এই ‘ব্রাহ্মণ’ শব্দটা লইয়া একটু গোল আছে। কারণ, ‘ব্রহ্ম’ শব্দটির ‘মন্ত্র’ অর্থও নাকি হয়!
অধ্যাপক মহাশয় বলিতেছেন, ম্যাক্সমুলারের এত সাহস হয় নাই যে বলেন, ‘ছিলই না’, কিন্তু প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, হিন্দু চাতুর্বর্ণ্য বৈদিক যুগে ‘স্পষ্টতঃ বিদ্যমান ছিল না’; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের যে বিভিন্ন বৃত্তির কথা শুনা যায়—তাহার তত বাঁধাবাঁধি বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে তৎকালে আবির্ভূত হয় নাই—অর্থাৎ যোগ্যতা-অনুসারে যে-কোন লোক যে-কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিত।
আমার ত মনে হয়, পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার জোর করিয়া ‘ছিলই না’ না বলিয়া নিজের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাতেই শুধু অর্জিত হয়। কিন্তু প্রত্যুত্তরে ভববিভূতিবাবু বলিতেছেন,—“সায়ণ চতুর্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়া না হয় তাঁহার ব্যাখ্যা উড়াইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইতে পার, কিন্তু সেই অপৌরুষেয় বেদেরই অন্তর্গত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ যখন ‘ব্রহ্মণস্পতি’ অর্থে ব্রাহ্মণপুরোহিত। [ ঐ. ব্রা. ৮। ৫। ২৪, ২৬ ] করিলেন, তখন তাহা কি বলিয়া উড়াইয়া দিবে? ব্রহ্মণ্যশক্তি যে সমাজ ও রাজশক্তির নিয়ন্ত্রী ছিল, তাহা আমরা ঋগ্বেদেই দেখিতে পাই!”
পাওয়াই ত উচিত। কিন্তু কে উড়াইয়া দিতেছে এবং দিবার প্রয়োজনই বা কি হইয়াছে, তাহা ত বুঝা গেল না! ব্রাহ্মণ পুরোহিত—বেশ ত! পুরোহিতের কাজ যিনি করিতেন, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা হইত। যজন-যাজন করিলে ব্রাহ্মণ বলিত; যুদ্ধ, রাজ্য-পালন করিলে ক্ষত্রিয় বলিত—এ কথা ত তাঁহারা কোথাও অস্বীকার করেন নাই। আদালতে বসিয়া যাঁহারা বিচার করেন, তাঁহাদিগকে জজ বলে, উকিল বলে না। শ্রীযুক্ত গুরুদাসবাবু যখন ওকালতি করিতেন, তাঁহাকে লোকে উকিল বলিত, জজ হইলে জজ বলিত।
ইহাতে আশ্চর্য হইবার আছে কি? ব্রাহ্মণ্যশক্তি বৈদিক যুগে রাজশক্তির নিয়ন্ত্রী ছিল। ইংরাজের আমলে বড়লাট ও মেম্বারেরা তাহাই, সুতরাং এই মেম্বারেরা রাজশক্তির নিয়ন্ত্রী ছিল বলিয়া একটা কথা যদি ভারতবর্ষের ইংরাজী ইতিহাসে পাওয়া যায় ত তাহাতে বিস্মিত হইবার বা তর্ক করিবার আছে কি? অথচ লাটের ছেলেরা লাটও হয় না, মেম্বার বলিয়াও কোন স্বতন্ত্র জাতির অস্তিত্ব নাই। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের প্রাচীনতা সম্বন্ধে শুনিতে পাই, নানাপ্রকার মতভেদ আছে। এই সম্পর্কে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার একটি অতিবড় অপকর্ম করিয়াছেন—তিনি লিখিয়াছেন—“কবষ শূদ্র হইয়াও দশম মণ্ডলের অনেকগুলি মন্ত্রের প্রণেতা (?)।”
‘দ্রষ্টা’ বলা তাঁহার উচিত ছিল। এই হেতু ভববিভূতিবাবু ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়া (?) চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছেন।
কিন্তু আমি বলি, বিদেশীর সম্বন্ধে অত খুঁটিনাটি ধরিতে নাই। কারণ, এই দশম মণ্ডলেরই ৮৫ সূক্তে সোম ও সূর্যের বিবাহ বর্ণনা করিয়া তিনি নিজেই বলিয়াছেন, এমন পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে আকাশের গ্রহ-তারার সম্বন্ধ বাঁধিবার চেষ্টা জগতের আর কোন সাহিত্যে দেখা যায় কি? এমন চেষ্টা জগতের আর কোন সাহিত্যে দেখা না যাইতে পারে; কিন্তু কোন একটা উদ্দেশ্য সাধন করিবার অভিপ্রায় বৈদিক কবিকে যে শ্লোকটি বিশেষ করিয়া সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল, তাহাকে বিদেশীয় কেহ যদি সেই কবির রচিত বলিয়া মনে করে, তাহাতে রাগ করিতে আছে কি? কিন্তু সে যাই হোক, সূক্তটি যে রূপকমাত্র, তাহা ভববিভূতিবাবু নিজেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। সুতরাং, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, অপৌরুষেয় বেদের অন্তর্গত সূক্তরাশির মধ্যেও এমন সূক্ত রহিয়াছে, যাহা রূপকমাত্র, অতএব খাঁটি সত্য হইতে বাছিয়া ফেলা অত্যাবশ্যক। এই অত্যাবশ্যক কাজটি যাহাকে দিয়া করাইতে হইবে, সে বস্তু কিন্তু বিশ্বাসপরায়ণতা বা ভক্তি নহে—সে মানুষের সংশয় এবং তর্কবুদ্ধি! অতএব ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তাহাকেই সকলের উপর স্থান দান করিতেই হইবে। না করিলে মানুষ মানুষই হইতে পারে না। কিন্তু, এই মনুষ্যত্ব চিরদিন সমভাবে থাকে না—সেইজন্য ইহাও কল্পনা করা অসম্ভব নয় যে, হয়ত এই ভারতেই একদিন ছিল, যখন এই চন্দ্র ও সূর্যের বিবাহ-ব্যাপারটা খাঁটি সত্য ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিতে মানুষ ইতস্ততঃ করে নাই। আবার আজ যাহাকে সত্য বলিয়া আমরা অসংশয়ে বিশ্বাস করিতেছি, তাহাকেই হয়ত আমাদের বংশধরেরা রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিবে! আজ আমরা জানি, সূর্য এবং চন্দ্র কি বস্তু এবং এইরূপ বিবাহ-ব্যাপারটাও কিরূপ অসম্ভব; তাই ইহাকে রূপক বলিতেছি। কিন্তু এই সূক্তই যদি আজ কোন পল্লীবাসিনী বৃদ্ধা নারীর কাছে বিবৃত করিয়া বলি, তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করিবেন না। কিন্তু তাহাতে কি বেদের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিবে? ভববিভূতিবাবু ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯০ সূক্ত উদ্ধৃত করিতে গিয়া কঠিন হইয়া বলিতেছেন,—“ইহাতেও কাহারও সন্দেহ থাকিলে তাহার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দশম মণ্ডলের ৯০ সূক্ত বা প্রখ্যাত ‘পুরুষসূক্তের’ দ্বাদশ ঋক্টি দেখাইয়া দিব, যথা—
ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্বৈস্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।।
অর্থ—সেই পরমপুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে রাজন্য বা ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল। ইহার অপেক্ষা চাতুর্ব্বর্ণ্যের আর স্পষ্ট উল্লেখ কি হইতে পারে?”
এই সূক্তটির বিচার পরে হইবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের উদ্দেশ্য ভববিভূতিবাবু যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ইনি বলিতেছেন যে, “আমাদের চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথার অর্ব্বাচীনতা প্রতিপন্ন করিয়া আমাদের ভারতীয় সভ্যতাকে আধুনিকরূপে জগৎসমক্ষে প্রচার করা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের প্রধান উদ্দেশ্য হইতে পারে এবং সেই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া ইত্যাদি—”
এরূপ উদ্দেশ্যকে সকলেই নিন্দা করিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সমস্ত উদ্দেশ্যেরই একটা অর্থ থাকে। এখানে অর্থটা কি? একটা সত্য বস্তুর কদর্থ বা কু-অর্থ করার হেয় উপায় অবলম্বন করিয়া চাতুর্বর্ণ্যকে বৈদিক যুগ হইতে নির্বাসিত করিয়া তাহাকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রতিপন্ন করায় এই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের লাভটা কি? শুধু চাতুর্বর্ণ্যই কি সভ্যতা? ইহাই কি বেদের সর্বপ্রধান রত্ন? চাতুর্বর্ণ্য বৈদিক যুগে থাকার প্রমাণ আমরা দাখিল না করিতে পারিলেই কি জগৎসমক্ষে প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে যে, আমাদের পিতামহেরা বৈদিক যুগে অসভ্য ছিল? পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মিশর, বেবিলন প্রভৃতি দেশের সভ্যতা ৮।১০ হাজার বৎসর পূর্বের বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের বেলাই তাঁহাদের এতটা নীচতা প্রকাশ করিবার হেতু কি?
তা ছাড়া, অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার ঋক্বেদের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত ভববিভূতিবাবুর এই মন্তব্য খাপ খায় না। আমার ঠিক স্মরণ হইতেছে না (এবং বইখানাও হাতের কাছে নাই), কিন্তু মনে যেন পড়িতেছে, তিনি Kant-এর Critique of the Pure Reason-এর ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—জগতে আসিয়া যদি কিছু শিখিয়া থাকি ত সে ঋক্বেদ ও এই Critique হইতে। একটা গ্রন্থের ভূমিকায় আর একটা গ্রন্থের উল্লেখ এমন অযাচিতভাবে করা সহজ শ্রদ্ধার কথা নয়।
তবে যে কেন তিনি ইহাকেই খাটো করিয়া দিবার প্রয়াস করিয়া আশাতীত সঙ্কীর্ণ অন্তঃকরণের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভববিভূতিবাবু বলিতে পারেন। যাই হউক, এই ‘হিন্দুজাতির প্রাণস্বরূপ’ ১০ম মণ্ডলের ৯০ সূক্তটি অপৌরুষেয় ঋক্বেদেরই অন্তর্গত থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পদাঙ্কানুসারী বঙ্গীয় অনুবাদক তাহাকে প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করায় ভববিভূতি মহাশয় “বড়ই কাতরকণ্ঠে দেশের আশা-ভরসাস্থল ছাত্রবৃন্দ ব্রাহ্মণতনয়গণ” কে ডাকাডাকি করিতেছেন, সেই সূক্তটি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহাকেও ডাক দেওয়া উচিত নয়। ইতিপূর্বেই এই ১০ম মণ্ডলেরই ৮৫ সূক্ত সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া গিয়াছে; তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রখ্যাত ৯০ সূক্তটি কি? ইহা পরমপুরুষের মুখ-হাত-পা দিয়া ব্রাহ্মণ প্রভৃতির তৈরী হওয়ার কথা।
কিন্তু ইহা জটাপাঠ, পদপাঠ, শাকল, বাস্কল দিয়া যতই যাচাই হইয়া গিয়া থাকুক না কেন, বিশ্বাস করিতে হইলে অন্ততঃ আরও শ-চারেক বৎসর পিছাইয়া যাওয়া আবশ্যক। কিন্তু সে যখন সম্ভব নহে, তখন আধুনিক কালে সংসারের চৌদ্দ আনা শিক্ষিত সভ্য লোক যাহা বিশ্বাস করেন—সেই অভিব্যক্তির পর্যায়েই মানুষের জন্ম হইয়াছে বলিয়া মানিতে হইবে। তার পর কোটি কোটি বৎসর নানাভাবে তাহার দিন কাটিয়া, শুধু কাল, না হয় পরশু সে সভ্যতার মুখ দেখিয়াছে। এ-পৃথিবীর উপর মানবজন্মের তুলনায় চাতুর্বর্ণ্য ঋগ্বেদে থাকুক আর না-থাকুক, সে কালকের কথা। অতএব হিন্দুজাতির প্রাণস্বরূপ এই সূক্তটিতে চাতুর্বর্ণ্যের সৃষ্টি যেভাবে দৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা প্রক্ষিপ্ত না হইলেও খাঁটি সত্য জিনিস নয়—রূপক।
কিন্তু ভয়ানক মিথ্যা, তদপেক্ষা ভয়ানক সত্য-মিথ্যায় মিশাইয়া দেওয়া। কারণ, ইহাতে না পারা যায় সহজে মিথ্যাকে বর্জন করা, না যায় নিষ্কলঙ্ক সত্যকে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধায় গ্রহণ করা। অতএব, এই রূপকের মধ্য হইতে নীর ত্যজিয়া ক্ষীর শোষণ করা বুদ্ধির কাজ। সেই বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে একজন যদি ইহার প্রতি অক্ষরটিকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে করে এবং আর একজন সমস্ত সূক্তটিকে মিথ্যা বলিয়া ত্যাগ করিতে উদ্যত হয়, তখন অপৌরুষেয়ের দোহাই দিয়া তাহাকে ঠেকাইবে কি করিয়া? সে যদি কহিতে থাকে, ইহাতে ব্রাহ্মণের ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, বৈশ্যের ধর্ম, শূদ্রের ধর্ম—এই চারি প্রকার নির্দেশ করা হইয়াছে, জাতি বা মানুষ নয় অর্থাৎ সেই পরমপুরুষের মুখ হইতে যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রভৃতি এক শ্রেণীর বৃত্তি; তাহাকে ব্রহ্মণ্যধর্ম বা ব্রাহ্মণ বলিবে। হাত হইতে ক্ষত্রিয়—অর্থাৎ বল বা শক্তির ধর্ম। এই প্রকার অর্থ যদি কেহ গ্রহণ করিতে চাহে, তাহাকে ‘না’ বলিয়া উড়াইয়া দিবে কি করিয়া? কিন্তু এইখানে একটা প্রশ্ন করিতে চাহি। এই যে এতক্ষণ ধরিয়া ঠোকাঠুকি কাটাকাটি করিয়া কথার শ্রাদ্ধ হইয়া গেল, তাহা কাহার কি কাজে আসিল? মনের অগোচর ত পাপ নাই? কতকটা বিদ্যা প্রকাশ করা ভিন্ন কোন পক্ষের আর কোন কাজ হইল কি? পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যদি বলিয়াইছিলেন, চাতুর্ব্বণ্য হিন্দুর বিরাট ভ্রম এবং অধঃপতনের অন্যতম কারণ এবং ইহা ঋক্বেদের সময়েও ছিল না—তবে ভববিভূতিবাবু যদি প্রতিবাদই করিলেন, তবে শুধু গায়ের জোরে তাঁদের কথাগুলা উড়াইয়া দিবার ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া কেন প্রমাণ করিয়া দিলেন না, এ প্রথা বেদে আছে। কারণ, বেদ অপৌরুষেয়, তাহার ভুল হইতে পারে না—জাতিভেদ প্রথা সুশৃঙ্খলার সহিত সমাজ-পরিচালনের যে সত্য সত্যই একমাত্র উপায়, তাহা এই সব বৈজ্ঞানিক, সামাজিক এবং ঐতিহাসিক নজির তুলিয়া দিয়া প্রমাণ করিয়া দিলাম।
তবে ত তাল ঠুকিয়া বলা যাইতে পারিত, এই দেখ, আমাদের অপৌরুষেয় বেদে যাহা আছে, তাহা মিথ্যাও নয় এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া হিন্দু ভুলও করে নাই, অধঃপথেও যায় নাই। তা যদি না করিলেন, তবে তাঁহারা জাতিভেদকে ভ্রমই বলুন আর যাই বলুন, সে-কথার উল্লেখ করিয়া শুধু শ্লোকের নজির তুলিয়া উহাদিগকে কানা বলিয়া, সঙ্কীর্ণচেতা বলিয়া, আর রাশি রাশি হা-হুতাশ উচ্ছ্বাসের প্রবাহ বহাইয়া দিয়াই কি কোন কাজ হইবে? বেদের মধ্যে যখন রূপকের স্থান রহিয়াছে, তখন বুদ্ধি-বিচারের অবকাশ আছে। সুতরাং শুধু উক্তিকেই অকাট্য যুক্তি বলিয়া দাঁড় করানো যাইবে না। আমি এই কথাটাই আমার এই ভূমিকায় বলিতে চাহিয়াছি।
অতঃপর হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কার বিবাহের কথা। ইনি প্রথমেই বলিতেছেন, “হিন্দুর এই পবিত্র বিবাহপদ্ধতি বহু সহস্র বৎসর পূর্বে,—ঋগ্বেদের সময়ে যেভাবে নিষ্পন্ন হইত, আজও—একালের বৈদেশিক সভ্যতার সংঘর্ষেও তাহা অণুমাত্র পরিবর্তিত হয় নাই।” অণুমাত্রও পরিবর্তিত যে হয় নাই, তাহা নিম্নলিখিত উদাহরণে সুস্পষ্ট করিয়াছেন—
“তখনও বরকে কন্যার গৃহে গিয়া বিবাহ করিতে হইত,—এখনও তাহা হইয়া থাকে। আবার বিবাহের পর শোভাযাত্রা করিয়া, বহুবিধ অলঙ্কারভূষিতা কন্যাকে লইয়া শ্বশুর-দত্ত নানাবিধ যৌতুক সহিত তখনও যেমন বর গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন, এখনও সেইরূপ হইয়া থাকে। বিবাহযোগ্যকালে কন্যা-সম্প্রদানের ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু ঐ বয়সের কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট নাই। কন্যা শ্বশুরালয়ে আসিয়া কর্ত্রীর স্থান অধিকার করিতেন, এবং শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর ও ননদগণের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতেন অর্থাৎ সকলকে বশ করিতেন।”
অতঃপর এই সকল উক্তি সপ্রমাণ করিতে নানাবিধ শ্লোক ও তাহার মন্তব্য লিখিয়া দিয়া বোধ করি অসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, এই সকল আচার-ব্যবহার বৈদিক কালে প্রচলিত ছিলই। ভালই।
কিন্তু এই যে বলিয়াছেন—বহু সহস্র বর্ষ পূর্বের বিবাহপদ্ধতি যেমনটি ছিল, আজও এই বৈদেশিক সভ্যতার সংঘর্ষেও ঠিক তেমনটি আছে, ‘অণুমাত্র’ পরিবর্তিত হয় নাই—ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। কারণ, পরিবর্তিত না হওয়ায় বলিতেই হইবে, আজকাল প্রচলিত বিবাহপদ্ধতিটিও ঠিক তেমনি নির্দোষ এবং ইহাই বোধ করি বলার তাৎপর্য। কিন্তু এই তাৎপর্যটির সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে না। বলিতেছেন,—“কন্যা-সম্প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কন্যার বয়সের কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট নাই।”
অর্থাৎ বুঝা যাইতেছে, আজকাল যেমন মেয়ের বয়স বারো উত্তীর্ণ হইয়া তেরোয় পড়িলেই ভয়ে এবং ভাবনায় মেয়ের বাপ-মায়ের জীবন দুর্ভর হইয়া উঠে এবং পাছে চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ এবং সমাজে ‘একঘরে’ হইয়া থাকিতে হয়, সেই ভয় ও ভাবনায় বাড়িসুদ্ধ লোকের পেটের ভাত চাল হইতে থাকে, তখনকার বৈদিক কালে এমনটি হইতে পারিত না। ইচ্ছামত বা সুবিধামত মেয়েকে ১২। ১৪। ১৮। ২০ যে-কোন বয়সেই হউক, পাত্রস্থ করা যাইতে পারিত। আর এমন না হইলে কন্যা শ্বশুরবাড়ি গিয়াই যে শ্বশুর-শাশুড়ি, ননদ-দেবরের উপর প্রভু হইয়া বসিয়া যাইত, সে নেহাত কচি খুকীটির কর্ম নয় ত।
রাগ দ্বেষ অভিমান গৃহিণীপনার ইচ্ছা প্রভৃতি যে সেকালে ছিল না—বউ বাড়ি ঢুকিবামাত্রই তাঁহার হাতে লোহার সিন্দুকের চাবিটি শাশুড়ী ননদে তুলিয়া দিত, সেও ত মনে করা যায় না।
যাই হউক, ভববিভূতিবাবুর নিজের কথা মত বয়সের কড়াকড়ি তখন ছিল না। কিন্তু এখন কড়াকড়িটা যে কি ব্যাপার, তাহা আর কোন ব্যক্তিকেই বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই বোধ করি।
দ্বিতীয়ঃ, ইনি বলিয়াছেন যে, “এই সকল উপঢৌকন কেহ যেন বর্তমানকালে প্রচলিত কদর্য পণপ্রথার প্রমাণরূপে গ্রহণ না করেন। এগুলি কন্যার পিতার স্বেচ্ছাকৃত, সামর্থ্যানুরূপ দান বুঝিতে হইবে।”
কিন্তু এখনকার উপঢৌকন যোগাইতে অনেক পিতাকে বাস্তুভিটাটি পর্যন্ত বেচিতে হয়। সে সময় কিন্তু অপৌরুষেয় ঋক্মন্ত্র মেয়ের বাপেরও এক তিল কাজে আসে না, বরের বাপকেও বিন্দুমাত্র ভয় দেখাইতে, তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না।
তৃতীয়তঃ, রাশীকৃত শাস্ত্রীয় বিচার করিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, যে-মেয়ের ভাই ছিল না, সে মেয়ের সহিত তখনকার দিনে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। এবং বলিতেছেন, অথচ, আজকাল এই বিবাহই সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক। কারণ, বিষয়-আশয় পাওয়া যায়। যদিচ, এতগুলি শাস্ত্রীয় শ্লোক ও তাহার অর্থাদি দেওয়া সত্ত্বেও মোটাবুদ্ধিতে আসিল না, ভাই না হওয়ায় বোনের অপরাধ কি এবং কেনই বা সে ত্যাজ্যা হইয়াছিল; কিন্তু এখন যখন ইহাই সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, তখন ইহাকেও একটা পরিবর্তন বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। তবেই দেখা যাইতেছে,
(১) তখন মেয়ের বিবাহের বয়স নির্দিষ্ট ছিল না, এখন ইহাই হইয়াছে বাপ-মায়ের মৃত্যুবাণ।
(২) স্বেচ্ছাকৃত উপঢৌকন দাঁড়াইয়াছে বাস্তুভিটা বেচা এবং
(৩) নিষিদ্ধ কন্যা হইয়াছেন সবচেয়ে সুসিদ্ধ মেয়ে।
ভববিভূতিবাবু বলিবেন, তা হোক না, কিন্তু এখনও ত বরকে সেই মেয়ের বাড়িতে গিয়াই বিবাহ করিতে হয় এবং শোভাযাত্রা করিয়া ঘরে ফিরিতে হয়। এ ত আর বৈদেশিক সভ্যতার সংঘর্ষ একতিল পরিবর্তিত করিতে পারে নাই? তা পারে নাই সত্য, তবুও মনে পড়ে, সেই যে কে একজন খুব খুশী হইয়া বলিয়াছিল,—“অন্নবস্ত্রের দুঃখ ছাড়া আর দুঃখ আমার সংসারে নেই!”
আবার ইহাই সব নয়। “বিবাহিতা পত্নী যে গৃহের প্রধান অঙ্গ,—গৃহিণীর অভাবে যে গৃহ জীর্ণারণ্যের তুল্য”, তাহা ভট্টাচার্য্য মহাশয় “গৃহিণী গৃহমুচ্যতে”—এই প্রসিদ্ধ প্রবাদবাক্য হইতে সম্প্রতি অবগত হইয়াছেন। আবার ঋগ্বেদ পাঠেও এই প্রবাদটির সুপুরাতনত্বই সূচিত হইয়াছে। যথা—[৩ ম, ৫৩ সূ, ৪ ঋক্]
“জায়েদস্তং মঘবন্ত্ সেদু যোনিঃ”
অর্থাৎ হে মঘবন্—জায়াই গৃহ, জায়াই যোনি। সুতরাং বহু প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দুগণ রমণীগণের প্রতি আদর ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। আবার তাঁহাদের পত্নী কিরূপ মঙ্গলময়ী, তাহা “কল্যাণীর্জায়া … গৃহে তে” [৩ ম, ৫৩ সূ, ৬ ঋক্] হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয়। সুতরাং—
“কিন্তু তথাপি বৈদেশিকগণ কেন যে হিন্দুগণের উপর রমণীগণের প্রতি কঠোর ব্যবহারের জন্য দোষারোপ করেন, তাহা তাঁহারাই জানেন।”
এই সকল প্রবন্ধ ও মতামতের যে প্রতিবাদ করা আবশ্যক, সে কথা অবশ্য কেহই বলিবেন না। আমিও একেবারেই করিতাম না, যদি না ইহা আমার প্রবন্ধের ভূমিকা হিসাবেও কাজে লাগিত। তথাপি প্রতিবাদ করিতে আমি চাহি না — কিন্তু ইহারই মত ‘বড় কাতরকণ্ঠে’ ডাকিতে চাহি—ভগবন্! এই সমস্ত শ্লোক আওড়ানোর হাত হইতে এই হতভাগ্য দেশকে রেহাই দাও। ঢের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া লইয়াছ, এইবার একটু নিষ্কৃতি দাও। -শ্রীমতী অনিলা দেবী ( ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩)
সমাজ-ধর্মের মূল্য
বিড়ালকে মার্জার বলিয়া বুঝাইবার প্রয়াস করায় পাণ্ডিত্য প্রকাশ যদি বা পায়, তথাপি পণ্ডিতের কাণ্ডজ্ঞান সম্বন্ধে লোকের যে দারুণ সংশয় উপস্থিত হইবে, তাহা আমি নিশ্চয় জানি। জানি বলিয়াই, প্রবন্ধ লেখার প্রচলিত পদ্ধতি যাই হউক, প্রথমেই ‘সমাজ’ কথাটা বুঝাইবার জন্য ইহার ব্যুৎপত্তিগত এবং উৎপত্তিগত ইতিহাস বিবৃত করিয়া, বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া, অবশেষে ইহা এ নয়, ও নয়, তা নয়—বলিয়া পাঠকের চিত্ত বিভ্রান্ত করিয়া দিয়া গবেষণাপূর্ণ উপসংহার করিতে আমি নারাজ। আমি জানি, এ প্রবন্ধ পড়িতে যাঁহার ধৈর্য থাকিবে, তাঁহাকে ‘সমাজের’ মানে বুঝাইতে হইবে না। দলবদ্ধ হইয়া বাস করার নামই যে সমাজ নয়—মৌরোলা মাছের ঝাঁক, মৌমাছির চাক, পিঁপড়ার বাসা বা বীর হনুমানের মস্ত দলটাকে যে ‘সমাজ’ বলে না, এ খবর আমার নিকট হইতে এই তিনি নূতন শুনিবেন না।
তবে, কেহ যদি বলেন, ‘সমাজ’ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ঝাপসা গোছের ধারণা মানুষের থাকিতে পারে বটে, কিন্তু তাই বলিয়া সূক্ষ্ম অর্থ প্রকাশ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করা কি প্রবন্ধকারের উচিত নয়? তাঁহাদের কাছে আমার বক্তব্য এই যে, না। কারণ সংসারে অনেক বস্তু আছে, যাহার মোটামুটি ঝাপসা ধারণাটাই সত্য বস্তু,—সূক্ষ্ম করিয়া দেখাইতে যাওয়া শুধু বিড়ম্বনা নয়, ফাঁকি দেওয়া ! ‘ঈশ্বর’ বলিলে যে ধারণাটা মানুষের হয়, সেটা অত্যন্তই মোটা, কিন্তু সেইটাই কাজের জিনিস। এই মোটার উপরেই দুনিয়া চলে, সূক্ষ্মের উপর নয়। সমাজও ঠিক তাই। একজন অশিক্ষিত পাড়াগাঁয়ের চাষা ‘সমাজ’ বলিয়া যাহাকে জানে, তাহার উপরেই নির্ভয়ে ভর দেওয়া চলে—পণ্ডিতের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যাটির উপরে চলে না। অন্ততঃ আমি বোঝাপড়া করিতে চাই এই মোটা বস্তুটিকে লইয়াই। যে সমাজ মড়া মরিলে কাঁধ দিতে আসে, আবার শ্রাদ্ধের সময় দলাদলি পাকায়; বিবাহে যে ঘটকালি করিয়া দেয়, অথচ বউভাতে হয়ত বাঁকিয়া বসে; কাজকর্মে, হাতে-পায়ে ধরিয়া যাহার ক্রোধ শান্তি করিতে হয়, উৎসবে-ব্যসনে যে সাহায্যও করে, বিবাদও করে; যে সহস্র দোষত্রুটি সত্ত্বেও পূজনীয়—আমি তাহাকেই সমাজ বলিতেছি এবং এই সমাজ যদ্দ্বারা শাসিত হয়, সেই বস্তুটিকেই সমাজ-ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিতেছি। তবে, এইখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, যে ধর্ম নির্বিশেষে সকল দেশের, সকল জাতির সমাজকে শাসন করে, সেই সামাজিক ধর্মের আলোচনা করা আমার প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। কারণ, মানুষ মোটের উপর মানুষই। তাহার সুখ-দুঃখ আচার-ব্যবহারের ধারা সর্বদেশেই একদিকে চলে। মড়া মরিলে সব দেশেই প্রতিবেশীরা সৎকার করিতে জড় হয়; বিবাহে সর্বত্রই আনন্দ করিতে আসে; বাপ-মা সব দেশেই সন্তানের পূজ্য; বয়োবৃদ্ধের সম্মাননা সব দেশেরই নিয়ম; স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ সর্বত্রই প্রায়ই একরূপ; আতিথ্য সর্বদেশেই গৃহস্থের ধর্ম। প্রভেদ শুধু খুঁটিনাটিতে।
মৃতদেহে কেহ-বা গৃহ হইতে গাড়ি-পালকি করিয়া, ফুলের মালায় আবৃত করিয়া গোরস্থানে লইয়া যায়, কেহ-বা ছেঁড়া মাদুরে জড়াইয়া, বংশখণ্ডে বিচালির দড়ি দিয়া বাঁধিয়া, গোবরজলের সৌগন্ধ ছড়াইয়া ঝুলাইতে ঝুলাইতে লইয়া চলে; বিবাহ করিতে কোথাও-বা বরকে তরবারি প্রভৃতি পাঁচ হাতিয়ার বাঁধিয়া যাইতে হয়, আর কোথাও জাঁতিটি হাতে করিয়া গেলেই পাঁচ হাতিয়ারের কাজ হইতেছে মনে করা হয়। বস্ততঃ, এইসব ছোট জিনিস লইয়াই মানুষে মানুষে বাদ-বিতণ্ডা কলহ-বিবাদ। এবং যাহা বড়, প্রশস্ত, সমাজে বাস করিবার পক্ষে যাহা একান্ত প্রয়োজনীয়, সে সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই, হইতেও পারে না। আর পারে না বলিয়াই এখনও ভগবানের রাজ্য বজায় রহিয়াছে; মানুষ সংসারে আজীবন বাস করিয়া জীবনান্তে তাঁহারই পদাশ্রয়ে পৌঁছিবার ভরসা করিতেছে। অতএব মৃতদেহের সৎকার করিতে হয়, বিবাহ করিয়া সন্তান প্রতিপালন করিতে হয়, প্রতিবেশীকে সুবিধা পাইলেই খুন করিতে নাই, চুরি করা পাপ, এইসব স্থূল, অথচ অত্যাবশ্যক সামাজিক ধর্ম সবাই মানিতে বাধ্য; তা তাহার বাড়ি আফ্রিকার সাহারাতেই হউক, আর এশিয়ার সাইবিরিয়াতেই হউক। কিন্তু এই সকল আমার প্রধান আলোচ্য বিষয় নয়। অথচ, এমন কথাও বলি নাই, মনেও করি না যে, যাহা কিছু ছোট, তাহাই তুচ্ছ এবং আলোচনার অযোগ্য। পৃথিবীর যাবতীয় সমাজের সম্পর্কে ইহারা কাজে না আসিলেও বিচ্ছিন্ন এবং বিশেষ সমাজের মধ্যে ইহাদের যথেষ্ট কাজ আছে এবং সে কাজ তুচ্ছ নহে। সকল ক্ষেত্রেই এই সকল কর্মসমষ্টি—যা দেশাচাররূপে প্রকাশ পায়—তাহার যে অর্থ আছে, কিংবা সে অর্থ সুস্পষ্ট, তাহাও নহে; কিন্তু ইহারাই যে বিভিন্ন স্থানে সর্বজনীন সামাজিক ধর্মের বাহক, তাহাও কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। বহন করিবার এই সকল বিচিত্র ধারাগুলিকে চোখ মেলিয়া দেখাই আমার লক্ষ্য।
সামাজিক মানুষকে তিন প্রকার শাসন-পাশ আজীবন বহন করিতে হয়। প্রথম রাজ-শাসন, দ্বিতীয় নৈতিক-শাসন এবং তৃতীয় যাহাকে দেশাচার কহে, তাহারই শাসন।
রাজ-শাসন; আমি স্বেচ্ছাচারী দুর্বৃত্ত রাজার কথা বলিতেছি না—যে রাজা সুসভ্য, প্রজাবৎসল-তাঁহার শাসনের মধ্যে তাঁহার প্রজাবৃন্দেরই সমবেত ইচ্ছা প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে। তাই খুন করিয়া যখন সেই শাসন-পাশ গলায় বাঁধিয়া ফাঁসিকাঠে গিয়া উঠি, তখন সে ফাঁসের মধ্যে আমার নিজের ইচ্ছা যে প্রকারান্তরে মিশিয়া নাই, একথা বলা যায় না। অথচ মানবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশে আমার নিজের বেলা সেই নিজের ইচ্ছাকে যখন ফাঁকি দিয়া আত্মরক্ষা করিতে চাই, তখন যে আসিয়া জোর করে, সে-ই রাজশক্তি। শক্তি ব্যতীত শাসন হয় না। এমনি নীতি এবং দেশাচারকে মান্য করিতে যে আমাকে বাধ্য করে, সে-ই আমার সমাজ এবং সামাজিক আইন।
আইনের উদ্ভব সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রচলিত থাকিলেও মুখ্যতঃ রাজার সৃজিত আইন যেমন রাজা-প্রজা উভয়কেই নিয়ন্ত্রিত করে, নীতি ও দেশাচার তেমনি সমাজ-সৃষ্ট হইয়াও সমাজ ও সামাজিক মনুষ্য উভয়কেই নিয়ন্ত্রিত করে।
কিন্তু, এই আইনগুলি কি নির্ভুল? কেহই ত এমন কথা কহে না। ইহার মধ্যে কত অসম্পূর্ণতা, কত অন্যায়, কত অসঙ্গতি ও কঠোরতার শৃঙ্খল রহিয়াছে। নাই কোথায়? রাজার আইনের মধ্যেও আছে, সমাজের আইনের মধ্যেও রহিয়াছে।
এত থাকা সত্ত্বেও, আইন-সম্বন্ধে আলোচনা ও বিচার করিয়া যত লোক যত কথা বলিয়া গিয়াছেন—যদিচ আমি তাঁহাদের মতামত তুলিয়া এই প্রবন্ধের কলেবর ভারাক্রান্ত করিতে চাহি না—মোটের উপর তাঁহারা প্রত্যেকেই স্বীকার করিয়াছেন, আইন যতক্ষণ আইন,—তা ভুলভ্রান্তি তাহাতে যতই কেন থাকুক না, ততক্ষণ—শিরোধার্য তাহাকে করিতেই হইবে। না করার নাম বিদ্রোহ। এবং ”The righteousness of a cause is never alone a sufficient justification of rebellion.”
সামাজিক আইন-কানুন সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে না কি?
আমি আমাদের সমাজের কথাই বলি। রাজার আইন রাজা দেখিবেন, সে আমার বক্তব্য নয়। কিন্তু সামাজিক আইন-কানুনে-ভুলচুক অন্যায়-অসঙ্গতি কি আছে না-আছে, সে না হয় পরে দেখা যাইবে;—কিন্তু এই সকল থাকা সত্ত্বেও ত ইহাকে মানিয়া চলিতে হইবে। যতক্ষণ ইহা সামাজিক শাসন-বিধি, ততক্ষণ ত শুধু নিজের ন্যায্য দাবীর অছিলায় ইহাকে অতিক্রম করিয়া তুমুল কাণ্ড করিয়া তোলা যায় না। সমাজের অন্যায়, অসঙ্গতি, ভুলভ্রান্তি বিচার করিয়া সংশোধন করা যায়, কিন্তু তাহা না করিয়া শুধু নিজের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের বলে একা একা বা দুই চারিজন সঙ্গী লইয়া বিপ্লব বাধাইয়া দিয়া যে সমাজ-সংস্কারের সুফল পাওয়া যায়, তাহা ত কোনমতেই বলা যায় না।
শ্রীযুক্ত রবিবাবুর ‘গোরা’ বইখানি যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন, এই প্রকারের কিছু কিছু আলোচনা তাহাতে আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাহার কি মীমাংসা করা হইয়াছে, আমি জানি না। তবে, ন্যায়-পক্ষ হইলে এবং উদ্দেশ্য সাধু হইলে যেন দোষ নেই এই রকম মনে হয়। সত্যপ্রিয় পরেশবাবু সত্যকেই একমাত্র লক্ষ্য করিয়া বিপ্লবের সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই। ”সত্য” কথাটি শুনিতে মন্দ নয়, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাহার ঠিক চেহারাটি চিনিয়া বাহির করা কঠিন। কারণ, কোন পক্ষই মনে করে না যে, সে অসত্যের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে। উভয় পক্ষেরই ধারণা—সত্য তাহারই দিকে।
ইহাতে আরও একটি কথা বলা হইয়াছে যে, সমাজ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হাত দিতে পারে না। কারণ, ব্যক্তির স্বাধীনতা সমাজের জন্য সঙ্কুচিত হইতে পারে না। বরঞ্চ, সমাজকেই এই স্বাধীনতার স্থান যোগাইবার জন্য নিজেকে প্রসারিত করিতে হইবে। পণ্ডিত H. Spencer-এর মতও তাই। তবে, তিনি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এই বলিয়া সীমাবদ্ধ করিয়াছেন যে, যতক্ষণ না তাহা অপরের তুল্য স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে। কিন্তু, ভাল করিয়া দেখিতে গেলে, এই অপরের তুল্য স্বাধীনতায় যে কার্যক্ষেত্রে কতদিকে কতপ্রকারে টান ধরে, পরিশেষে ঐ ‘সত্য’ কথাটির মত কোথায় যে ‘সত্য’ আছে—তাহার কোন উদ্দেশই পাওয়া যায় না।
যাহা হউক, কথাটা মিথ্যা নয় যে, সামাজিক আইন বা রাজার আইন চিরদিন এমনি করিয়াই প্রসারিত হইয়াছে এবং হইতেছে। কিন্তু যতক্ষণ তাহা না হইতেছে, ততক্ষণ সমাজ যদি তাহার শাস্ত্র বা অন্যায় দেশাচারে কাহাকেও ক্লেশ দিতেই বাধ্য হয়, তাহার সংশোধন না করা পর্যন্ত এই অন্যায়ের পদতলে নিজের ন্যায্য দাবী বা স্বার্থ বলি দেওয়ায় যে কোন পৌরুষ নাই, তাহাতে যে কোন মঙ্গল হয় না, এমন কথাও ত জোর করিয়া বলা চলে না।
কথাটা শুনিতে হয়ত কতকটা হেঁয়ালির মত হইল। পরে তাহাকে পরিস্ফুট করিতে যত্ন করিব। কিন্তু এইখানে একটা মোটা কথা বলিয়া রাখি যে, রাজশক্তির বিপক্ষে বিদ্রোহ করিয়া তাহার বল ক্ষয় করিয়া তোলায় যেমন দেশের মঙ্গল নাই—একটা ভালর জন্য অনেক ভাল তাহাতে যেমন বিপর্যস্ত, লণ্ডভণ্ড হইয়া যায়, সমাজ-শক্তির সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাই খাটে। এই কথাটা কোনমতেই ভোলা চলে না যে, প্রতিবাদ এক বস্তু, কিন্তু বিদ্রোহ সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। বিদ্রোহকে চরম প্রতিবাদ বলিয়া কৈফিয়ত দেওয়া যায় না। কারণ, ইহা অনেকবার অনেক প্রকারে দেখা গিয়াছে যে, প্রতিষ্ঠিত শাসন-দণ্ডের উচ্ছেদ করিয়া তাহা অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ শাসন-দণ্ড প্রবর্তিত করিলেও কোন ফল হয় না, বরঞ্চ কুফলই ফলে।
আমাদের ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলে এই কথাটা অনেকটা বোঝা যায়। সেই সময়ের বাংলা দেশের সহস্র প্রকার অসঙ্গত, অমূলক ও অবোধ্য দেশাচারে বিরক্ত হইয়া কয়েকজন মহৎপ্রাণ মহাত্মা এই অন্যায়রাশির আমূল সংস্কারের তীব্র আকাঙ্ক্ষায়, প্রতিষ্ঠিত সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তিত করিয়া নিজেদের এরূপ বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন যে, তাহা নিজেদের যদি বা কাজে লাগিয়া থাকে, দেশের কোন কাজেই লাগিল না। দেশ তাঁহাদের বিদ্রোহী ম্লেচ্ছ খ্রীস্টান মনে করিতে লাগিল। তাঁহারা জাতিভেদ তুলিয়া দিলেন, আহারের আচার-বিচার মানিলেন না, সপ্তাহ অন্তে একদিন গির্জার মত সমাজগৃহে বা মন্দিরের মধ্যে জুতা-মোজা পায়ে দিয়া ভিড় করিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা এত বেশী সংস্কার করিয়া ফেলিলেন যে, তাঁহাদের সমস্ত কার্যকলাপই তৎকাল-প্রতিষ্ঠিত আচার-বিচারের সহিত একেবারে উলটা বলিয়া লোকের চক্ষে পড়িতে লাগিল। ইহা যে হিন্দুর পরম সম্পদ বেদমূলক ধর্ম, সে কথা কেহই বুঝিতে চাহিল না। আজও পাড়াগাঁয়ের লোক ব্রাহ্মদের খ্রীস্টান বলিয়াই মনে করে।
কিন্তু যে-সকল সংস্কার তাঁহারা প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছিলেন, দেশের লোক যদি তাহা নিজেদেরই দেশের জিনিস বলিয়া বুঝিতে পারিত এবং গ্রহণ করিত, তাহা হইলে আজ বাঙালী সমাজের এ দুর্দশা বোধ করি থাকিত না। অসীম দুঃখময় এই বিবাহ-সমস্যা, বিধবার সমস্যা, উন্নতিমূলক বিলাত-যাওয়া-সমস্যা, সমস্তই একসঙ্গে একটা নির্দিষ্ট কূলে আসিয়া পৌঁছিতে পারিত। অন্যপক্ষে গতি এবং বৃদ্ধিই যদি সজীবতার লক্ষণ হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, এই ব্রাহ্ম-সমাজও আজ মৃত্যুমুখে পতিত না হইলেও অকাল-বার্ধক্যে উপনীত হইয়াছে।
সংস্কার মানেই প্রতিষ্ঠিতের সহিত বিরোধ; এবং অত্যন্ত সংস্কারের চেষ্টাই চরম বিরোধ বা বিদ্রোহ। ব্রাহ্ম-সমাজ এ কথা বিস্মৃত হইয়া অত্যল্পকালের মধ্যেই সংস্কার, রীতি-নীতি, আচার-বিচার সম্বন্ধে নিজেদের এতটাই স্বতন্ত্র এবং উন্নত করিয়া ফেলিলেন যে, হিন্দু-সমাজ হঠাৎ তীব্র ক্রোধ ভুলিয়া হাসিয়া ফেলিল এবং নিজেদের অবসরকালে ইহাদিগকে লইয়া এখানে ওখানে বেশ একটু আমোদ করিতেও লাগিল।
হায় রে! এমন ধর্ম, এমন সমাজ, পরিশেষে কিনা পরিহাসের বস্তু হইয়া উঠিল! জানি না, এই পরিহাসের জরিমানা কোনদিন হিন্দুকে সুদ-সুদ্ধ উসুল দিতে হইবে কি না। কিন্তু ব্রাহ্মই বল, আর হিন্দুই বল, বাংলার বাঙালী-সমাজকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল দুই দিক দিয়াই।
আরও একটা কথা এই যে, সামাজিক আইন-কানুন প্রতিষ্ঠিত হয় যে দিক দিয়া, তাহার সংস্কারও হওয়া চাই সেই দিক দিয়া; শাসন-দণ্ড পরিচালন করেন যাঁহারা, সংস্কার করিবেন তাঁহারাই। অর্থাৎ, মনু-পরাশরের বিধিনিষেধ মনু-পরাশরের দিক দিয়াই সংস্কৃত হওয়া চাই। বাইবেল কোরান হাজার ভাল হইলেও কোন কাজেই আসিবে না। দেশের ব্রাহ্মণেরাই যদি সমাজ-যন্ত্র এতাবৎকাল পরিচালন করিয়া আসিয়া থাকেন, ইহার মেরামতি-কার্য তাঁহাদিগকে দিয়াই করাইয়া লইতে হইবে। এখানে হাইকোর্টের জজেরা হাজার বিচক্ষণ হওয়া সত্ত্বেও কোন সাহায্যই করিতে পারিবেন না। দেশের লোক এ-বিষয়ে পুরুষানুক্রমে যাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে অভ্যাস করিয়াছে—হাজার বদ অভ্যাস হইলেও সে অভ্যাস তাহারা ছাড়িতে চাহিবে না!
এ-সকল স্থূল সত্য কথা। সুতরাং আশা করি, এতক্ষণ যাহা বলিয়াছি, সে সম্বন্ধে বিশেষ কাহারো মতভেদ হইবে না।
যদি না হয়, তবে একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, মনু-পরাশরের হাত দিয়াই যদি হিন্দুর অবনতি পৌঁছিয়া থাকে ত উন্নতিও তাঁহাদের হাত দিয়াই পাইতে হইবে—অন্য কোন জাতির সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা, তা সে যত উন্নতই হউক, হিন্দুকে কিছুই দিতে পারিবে না। তুলনায় সমালোচনায় দোষগুণ কিছু দেখাইয়া দিতে আরে, এইমাত্র।
কিন্তু যে-কোন বিধি-ব্যবস্থা হউক, যাহা মানুষকে শাসন করে, তাহার দোষগুণ কি দিয়া বিচার করা যায়? তাহার সুখ-সৌভাগ্য দিবার ক্ষমতা দিয়া, কিংবা তাহার বিপদ ও দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করিবার ক্ষমতা দিয়া? Sir William Markly তাঁহার Elements of Law গ্রন্থে বলেন—“The value is to be measured not by the happiness which it procures, but by the misery from which it preserves us.” আমিও ইহাই বিশ্বাস করি। সুতরাং মনু-পরাশরের বিধি-ব্যবস্থা আমাদের কি সম্পদ দান করিয়াছে, সে তর্ক তুলিয়া নয়, কি বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে, শুধু সেই আলোচনা করিয়া সমাজের দোষগুণ বিচার করা উচিত। অতএব, আজও যদি আমাদের ঐ মনু-পরাশরের সংস্কার করাই আবশ্যক হইয়া থাকে, তবে ঐ ধারা ধরিয়াই করা চাই।
স্বর্গই হউক আর মোক্ষই হউক, সে কি দিতেছে, সে বিচার করিয়া নয়, বরঞ্চ সব বিপদ হইতে আজ আর সে আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারিতেছে না, শুধু সেই বিচার করিয়া। সুতরাং, হিন্দু যখন উপর দিকে চাহিয়া বলেন, ঐ দেখ আমাদের ধর্মশাস্ত্র স্বর্গের কবাট সোজা খুলিয়া দিয়াছেন, আমি তখন বলি—সেটা না হয় পরে দেখিয়ো, কিন্তু আপাততঃ নীচের দিকে চাহিয়া দেখ, নরকে পড়িবার দুয়ারটা সম্প্রতি বন্ধ করা হইয়াছে কি না। কারণ, এটা ওটার চেয়েও আবশ্যক। সহস্র বর্ষ পূর্বে হিন্দুশাস্ত্র স্বর্গপ্রবেশের যে সোজা পথটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সে পথটি আজও নিশ্চয় তেমনই আছে। সেখানে পৌঁছিয়া একদিন সেইরূপ আমোদ উপভোগ করিবার আশা বেশী কথা নয়—কিন্তু, নানাপ্রকার বিজাতীয় সভ্যতা অসভ্যতার সংঘর্ষে ইতিমধ্যে নীচে পড়িয়া পিষিয়া মরিবার যে নিত্য নূতন পথ খুলিয়া যাইতেছে, সেগুলি ঠেকাইবার কোনরূপ বিধি-ব্যবস্থা শাস্ত্রগ্রন্থে আছে কি না, সম্প্রতি তাহাই খুঁজিয়া দেখ। যদি না থাকে, প্রস্তুত কর; তাহাতেও দোষ নাই; বিপদে রক্ষা করাই ত আইনের কাজ। কিন্তু উদ্দেশ্য ও আবশ্যক যত বড় হউক, ‘প্রস্তুত’ শব্দটা শুনিবামাত্রই হয়ত পণ্ডিতদের দল চেঁচাইয়া উঠিবেন। আরে এ বলে কি! এ কি যার-তার শাস্ত্র যে, আবশ্যকমত দুটো কথা বানাইয়া লইব? এ যে হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থ! অপৌরুষেয়—অন্ততঃ ঋষিদের তৈরি, যাঁরা ভগবানের কৃপায় ভূত-ভবিষ্যৎ সমস্ত জানিয়া শুনিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এ কথা তাঁরা স্মরণ করেন না যে, এটা শুধু হিন্দুর উপরেই ভগবানের দয়া নয়—এমনি দয়া সব জাতির প্রতিই তিনি করিয়া গিয়াছেন। ইহুদিরাও বলে তাই, খ্রীস্টান, মুসলমান—তারাও তাই বলে। কেহই বলে না যে, তাহাদের ধর্ম এবং শাস্ত্রগ্রন্থ, সাধারণ মানুষের সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনার ফল। এ বিষয়ে হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থের বিশেষ কোন একটা বিশেষত্ব আমি ত দেখিতে পাই না। সকলেরই যেমন করিয়া পাওয়া, আমাদেরও তেমনি করিয়া পাওয়া। সে যাই হউক, আবশ্যক হইলে শাস্ত্রীয় শ্লোক একটা বদলাইয়া যদি আর একটা নাও করা যায়—নতুন একটা রচনা করিয়া বেশ দেওয়া যায়। এবং এমন কাণ্ড বহুবার হইয়াও গিয়াছে, তাহার অনেক প্রমাণ আছে। আর তাই যদি না হইবে, তবে যে-কোন একটা বিধি-নিষিধের এত প্রকার অর্থ, এত প্রকার তাৎপর্য পাওয়া যায় কেন?
এই “ভারতবর্ষ’’ কাগজেই অনেকদিন পূর্বে ডাক্তার শ্রীযুক্ত নরেশবাবু বলিয়াছিলেন, “না জানিয়া শাস্ত্রের দোহাই দিয়ো না!” কিন্তু, আমি ত বলি, সেই একমাত্র কাজ, যাহা শাস্ত্র না জানিয়া পারা যায়। কারণ, জানিলে তাহার আর শাস্ত্রের দোহাই পাড়িবার কিছুমাত্র জো থাকে না। তখন ‘বাঁশবনে ডোম কানা’ হওয়ার মত সে ত নিজেই কোনদিকে কূল-কিনারা খুঁজিয়া পায় না; সুতরাং, কথায় কথায় সে শাস্ত্রের দোহাই দিতেও যেমন পারে না, মতের অনৈক্য হইলেই বচনের মুগুর হাতে করিয়া তাড়িয়া মারিতে যাইতেও তাহার তেমনি লজ্জা করে।
এই কাজটা তাহারাই ভাল পারে, যাহাদের শাস্ত্রজ্ঞানের পুঁজি যৎসামান্য। এবং ঐ জোরে তাহারা অমন নিঃসঙ্কোচে শাস্ত্রের দোহাই মানিয়া নিজের মত গায়ের জোরে জাহির করে এবং নিজেদের বিদ্যার বাহিরে সমস্ত আচার-ব্যবহারই অশাস্ত্রীয় বলিয়া নিন্দা করে।
কিন্তু মানবের মনের গতি বিচিত্র। তাহার আশা–আকাঙ্ক্ষা অসংখ্য। তাহার সুখ–দুঃখের ধারণা বহুপ্রকার। কালের পরিবর্তন ও উন্নতি অবনতির তালে তালে সমাজের মধ্যে সে নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি করে। চিরদিন করিয়াছে এবং চিরদিনই করিবে। ইহার মধ্যে সমাজ যদি নিজেকে অদম্য অপরিবর্তনীয় কল্পনা করিয়া, ঋষিদের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির উপর বরাত দিয়া, নির্ভয়ে পাথরের মত কঠিন হইয়া থাকিবার সঙ্কল্প করে ত তাহাকে মরিতেই হইবে। এই নির্বুদ্ধিতার দোষে অনেক বিশিষ্ট সমাজও পৃথিবীর পৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এ দুর্ঘটনা বিরল নয়; কিন্তু, আমাদের এই সমাজ, মুখে সে যাই বলুক, কিন্তু কাজে যে সত্যিই মুনিঋষির ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির উপর নির্ভর করিয়া তাহার শাস্ত্র জিনিসটিকে লোহার শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখে নাই, তাহার সকলের চেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, সে সমাজ এখনও টিকিয়া আছে। বাহিরের সহিত ভিতরের সামঞ্জস্য রক্ষা করাই ত বাঁচিয়া থাকা। সুতরাং সে যখন বাঁচিয়া আছে, তখন যে–কোন উপায়ে, যে–কোন কলাকৌশলের দ্বারা সে যে এই সামঞ্জস্য করিয়া আসিয়াছে, তাহা ত স্বতঃসিদ্ধ।
সর্বত্রই সমস্ত বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই সামঞ্জস্য প্রধানতঃ যে উপায়ে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে—তাহা প্রকাশ্যে নূতন শ্লোক রচনা করিয়া নহে। কারণ, দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় জানা গিয়াছে যে, নব–রচিত শ্লোক বেনামীতে এবং প্রাচীনতার ছাপ লাগাইয়া চালাইয়া দিতে পারিলেই তবে ছুটিয়া চলে, না হইলে খোঁড়াইতে থাকে। অতএব, নিজের জোরে নূতন শ্লোক তৈরি করা প্রকৃষ্ট উপায় নহে। প্রকৃষ্ট উপায় ব্যাখ্যা।
তাহা হইলে দেখা যাইতেছে—পুরাতন সভ্য–সমাজের মধ্যে শুধু গ্রীক ও রোম ছাড়া আর সকল জাতি এই দাবী করিয়াছে,—তাহাদের শাস্ত্র ঈশ্বরের দান। অথচ, সকলকেই নিজেদের বর্ধনশীল সমাজের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য এই ঈশ্বরদত্ত শাস্ত্রের পরিসর ক্রমাগত বাড়াইয়া তুলিতে হইয়াছে। এবং সে–বিষয়ে সকলেই প্রায় এক পন্থাই অবলম্বন করিয়াছেন বর্তমান শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া।
কোন জিনিসের ইচ্ছামত ব্যাখ্যা করা যায় তিন প্রকারে। প্রথম—ব্যাকরণগত ধাতুপ্রত্যয়ের জোরে; দ্বিতীয়— পূর্বে এবং পরবর্তী শ্লোকের সহিত তাহার সম্বন্ধ বিচার করিয়া; এবং তৃতীয়—কোন বিশেষ দুঃখ দূর করিবার অভিপ্রায়ে শ্লোকটি সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় করিয়া। অর্থাৎ চেষ্টা করিলেই দেখা যায় যে, চিরদিন সমাজ–পরিচালকেরা নিজেদের হাতে এই তিনখানি হাতিয়ার—ব্যাকরণ, সম্বন্ধ এবং তাৎপর্য (positive and negative) লইয়া ঈশ্বরদত্ত যে–কোন শাস্ত্রীয় শ্লোকের যে–কোন অর্থ করিয়া পরবর্তী যুগের নিত্য নূতন সামাজিক প্রয়োজন ও তাহার ঋণ পরিশোধ করিয়া তাহাকে সজীব রাখিয়া আসিয়াছেন।
আজ যদি আমাদের জাতীয় ইতিহাস থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয় দেখিতে পাইতাম—কেন শাস্ত্রীয় বিধি–ব্যবস্থা এমন করিয়া পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে এবং কেনই বা এত মুনির এত রকম মত প্রচলিত হইয়াছে এবং কেনই বা প্রক্ষিপ্ত শ্লোকে শাস্ত্র বোঝাই হইয়া গিয়াছে। সমাজের এই ধারাবাহিক ইতিহাস নাই বলিয়াই এখন আমরা ধরিতে পারি না—অমুক শাস্ত্রের অমুক বিধি কিজন্য প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং কিজন্যই বা অমুক শাস্ত্রের দ্বারা তাহাই বাধিত হইয়াছিল। আজ সুদূরে দাঁড়াইয়া সবগুলি আমাদের চোখে এইরূপ দেখায়। কিন্তু, যদি তাহাদের নিকটে যাইয়া দেখিবার কোন পথ থাকিত ত নিশ্চয় দেখিতে পাইতাম—এই দুটি পরস্পর–বিরুদ্ধ বিধি একই স্থানে দাঁড়াইয়া আঁচড়া–আঁচড়ি করিতেছে না। একটি হয়ত আর–একটির শতবর্ষ পিছনে দাঁড়াইয়া ঠোঁটে আঙুল দিয়া নিঃশব্দে হাসিতেছে।
প্রবাহই জীবন। মানুষ যতক্ষণ বাঁচিয়া থাকে, ততক্ষণ একটা ধারা তাহার ভিতর দিয়া অনুক্ষণ বহিয়া যাইতে থাকে। বাহিরের প্রয়োজনীয়–অপ্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তুকে সে গ্রহণও করে, আবার ত্যাগও করে। যাহাতে তাহার আবশ্যক নাই, যে বস্তু দূষিত, তাহাকে পরিবর্জন করাই তাহার প্রাণের ধর্ম। কিন্তু মরিলে আর যখন ত্যাগ করিবার ক্ষমতা থাকিবে না, তখনই তাহাতে বাহির হইতে যাহা আসে, তাহারা কায়েম হইয়া বসিয়া যায় এবং মৃতদেহটাকে পচাইয়া তোলে। জীবন্ত সমাজ এ নিয়ম স্বভাবতই জানে। সে জানে, যে বস্তু আর তাহার কাজে লাগিতেছে না, মমতা করিয়া তাহাকে ঘরে রাখিলে মরিতেই হইবে। সে জানে, আবর্জনার মত তাহাকে ঝাঁটাইয়া না ফেলিয়া দিয়া, অনর্থক ভার বহিয়া বেড়াইলে অনর্থক শক্তিক্ষয় হইতে থাকিবে, এবং এই ক্ষয়ই একদিন তাহাকে মৃত্যুর মুখে ডালিয়া দিবে।
কিন্তু জীবনীশক্তি যত হ্রাস পাইতে থাকে, প্রবাহ যতই মন্দ হইতে মন্দতর হইয়া আসিতে থাকে, যতই তাহার দুর্বলতা দুষ্টের ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দিতে ভয় পায়, ততই তাহার ঘরে প্রয়োজনীয়–অপ্রয়োজনীয় ভাল– মন্দের বোঝা জমাট বাঁধিয়া উঠিতে থাকে। এবং সেই সমস্ত গুরুভার মাথায় লইয়া সেই জরাতুর মরণোন্মুখ সমাজকে কোনমতে লাঠিতে ভর দিয়া ধীরে ধীরে সেই শেষ আশ্রয় যমের বাড়ির পথেই যাইতে হয়।
ইহার কাছে এখন সমস্তই সমান—ভালও যা, মন্দও তাই; সাদাও যেমন, কালও তেমনই। কারণ জানিলে তবেই কাজ করা যায়, অবস্থার সহিত পরিচয় থাকিলেই তবে ব্যবস্থা করিতে পারা যায়। এখানকার এই জরাতুর সমাজ জানেই না—কিজন্য বিধি প্রবর্তিত হইয়াছিল, কেনই বা তাহা প্রকারান্তরে নিষিদ্ধ হইয়াছিল। মানুষের কোন্ দুঃখ সে দূর করিতে চাহিয়াছিল, কিংবা কোন্ পাপের আক্রমণ হইতে সে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এই অর্গল টানিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল। নিজের বিচার–শক্তি ইহার নাই, পরের কাছেও যে সমস্ত গন্ধমাদন তুলিয়া লইয়া হাজির করিবে—সে জোরও ইহার গিয়াছে। সুতরাং, এখন এ শুধু এই বলিয়া তর্ক করে যে, এই–সকল শাস্ত্রীয় বিধি– নিষেধ আমাদেরই ভগবান ও পরমপূজ্য মুনিঋষির তৈরি।
এই তপোবনেই তাঁরা মৃতসঞ্জীবনী লতাটি পুঁতিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং, যদিচ প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ও নিরর্থক ব্যাখ্যারূপ গুল্ম ও কণ্টকতৃণে এই তপোবনের মাঠটি সম্প্রতি সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই পরম শ্রেয়ঃ ইহারই মধ্যে কোথাও প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেই। অতএব আইস, হে সনাতন হিন্দুর দল, আমরা এই হোম–ধূম–পূত মাঠের সমস্ত ঘাস ও তৃণ চক্ষু মুদিয়া নির্বিকারে চর্বণ করিতে থাকি। আমরা অমৃতের পুত্র—সুতরাং সেই অমৃত–লতাটি একদিন যে আমাদের দীর্ঘ জিহ্বায় আটক খাইবেই, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই।
ইহাতে সংশয় না থাকিতে পারে। কিন্তু অমৃতের সকল সন্তানই কাঁচা ঘাস হজম করিতে পারিবে কি না, তাহাতেও কি সংশয় নাই!
কিন্তু আমি বলি, এই উদর এবং জিহ্বার উপর নির্ভর না করিয়া বুদ্ধি এবং দৃষ্টিশক্তির সাহায্য লইয়া কাঁটাগাছগুলা বাছিয়া ফেলিয়া, সেই অমৃত–লতাটির সন্ধান করিলে কি কাজটা অপেক্ষাকৃত সহজ এবং মানুষের মত দেখিতে হয় না?
ভগবান মানুষকে বুদ্ধি দিয়াছেন কিজন্য? সে কি শুধু আর একজনের লেখা শাস্ত্রীয় শ্লোক মুখস্থ করিবার জন্য? এবং একজন তাহার কি টীকা করিয়াছেন, এবং আর একজন সে টীকার কি অর্থ করিয়াছেন—তাহাই বুঝিবার জন্য? বুদ্ধির আর কি কোন স্বাধীন কাজ নাই? কিন্তু বুদ্ধির কথা তুলিলেই পণ্ডিতেরা লাফাইয়া উঠেন; ক্রুদ্ধ হইয়া বারংবার চীৎকার করিতে থাকেন। শাস্ত্রের মধ্যে বুদ্ধি খাটাইবে কোন্খানে? এ যে শাস্ত্র! তাঁদের বিশ্বাস, শাস্ত্রীয় বিচার শুধু শাস্ত্রকথার লড়াই। তাহার হেতু, কারণ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, সত্য, মিথ্যা, এ–সকল নিরূপণ করা নয়। শাস্ত্র– ব্যবসায়ীরা কতকাল হইতে যে এরূপ অবনত হীন হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা জানিবার উপায় নাই —কিন্তু এখন তাঁহাদের একমাত্র ধারণা যে, ব্রহ্মপুরাণের কুস্তির প্যাঁচ বায়ুপুরাণ দিয়া খসাইতে হইবে। আর পরাশরের লাঠির মার হারীতের লাঠিতে ঠেকাইতে হইবে। আর কোন পথ নাই। সুতরাং, যে ব্যক্তি এই কাজটা যত ভাল পারেন, তিনি তত বড় পণ্ডিত। ইহার মধ্যে শিক্ষিত ভদ্রব্যক্তির স্বাভাবিক সহজ বুদ্ধির কোন স্থানই নাই। কারণ, সে শ্লোক ও ভাষ্য মুখস্থ করে নাই।
অতএব, হে শিক্ষিত ভদ্রব্যক্তি! তুমি শুধু তোমাদের সমাজের নিরপেক্ষ দর্শকের মত মিটমিট করিয়া চাহিয়া থাক, এবং শাস্ত্রীয় বিচারের আসরে স্মৃতিরত্ন আর তর্করত্ন কণ্ঠস্থ শ্লোকের গদ্কা ভাঁজিয়া যখন আসর গরম করিয়া তুলিবেন, তখন হাততালি দাও।
কিন্তু তামাশা এই যে, জিজ্ঞাসা করিলে এইসব পণ্ডিতেরা বলিতেও পারিবেন না—কেন তাঁরা ও– রকম উন্মত্তের মত ওই যন্ত্রটা ঘুরাইয়া ফিরিতেছেন! এবং কি তাঁদের উদ্দেশ্য! কেনই বা এই আচারটা ভাল বলিতেছেন এবং কেনই বা এটার বিরুদ্ধে এমন বাঁকিয়া বসিতেছেন। যদি প্রশ্ন করা যায়, তখনকার দিনে যে উদ্দেশ্য বা যে দুঃখের নিষ্কৃতি দেবার জন্য অমুক বিধি–নিষেধ প্রবর্তিত হইয়াছিল—এখনও কি তাই আছে; ইহাতেই কি মঙ্গল হইবে? প্রত্যুত্তরে স্মৃতিরত্ন তাঁহার গদ্কা বাহির করিয়া তোমার সম্মুখে ঘুরাইতে থাকিবেন, যতক্ষণ না তুমি ভীত ও হতাশ হইয়া চলিয়া যাও।
এইখানে আমি একটি প্রবন্ধের বিস্তৃত সমালোচনা করিতে ইচ্ছা করি। কারণ, তাহাতে আপনা হইতেই অনেক কথা পরিস্ফুট হইবার সম্ভাবনা। প্রবন্ধটি অধ্যাপক শ্রীভববিভূতি ভট্টাচার্য বিদ্যাভূষণ এম. এ. লিখিত ‘ঋগ্বেদে চাতুর্ব্বণ্য ও আচার’ মাঘের ‘ভারতবর্ষে’ প্রথমেই ছাপা হইয়া বোধ করি, ইহা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।
কিন্তু আমি আকৃষ্ট হইয়াছি, ইহার শাস্ত্রীয় বিচারের সনাতন পদ্ধতিতে, ইহার ঝাঁজে এবং রৌদ্র, করুণ প্রভৃতি রসের উত্তাপে এবং উচ্ছ্বাসে।
প্রবন্ধটি পড়িয়া আমার স্বর্গীয় মহাত্মা রামমোহন রায়ের সেই কথাটি মনে পড়িয়া গিয়াছিল। শাস্ত্রীয় বিচারে যিনি মাথা গরম করেন, তিনি দুর্বল। এইজন্য একবার মনে করিয়াছিলাম, এই প্রবন্ধের সমালোচনা না করাই উচিত। কিন্তু ঠিক এই ধরনের আর কোন প্রবন্ধ হাতের কাছে না পাওয়ায় শেষে বাধ্য হইয়া ইহারই আলোচনাকে ভূমিকা করিতে হইল। কারণ, আমি যাহার মূল্য–নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহারই কতকটা আভাস এই ‘চাতুর্ব্বণ্য’ প্রবন্ধে দেওয়া হইয়াছে।
এই প্রবন্ধে ভববিভূতি মহাশয় স্বর্গীয় রমেশ দত্তের উপর ভারী খাপ্পা হইয়াছেন। প্রথম কারণ, তিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পদাঙ্কানুসারী দেশীয় বিদ্বানগণের অন্যতম। এই পাপে তাঁর টাইটেল দেওয়া হইয়াছে ‘পদাঙ্কানুসারী রমেশ দত্ত’—যেমন মহামহোপাধ্যায় অমুক, রায় বাহাদুর অমুক, এই প্রকার। যেখানেই স্বর্গীয় দত্ত মহাশয় উল্লিখিত হইয়াছেন, সেইখানেই এই টাইটেলটি বাদ যায় নাই। দ্বিতীয় এবং ক্রোধের মুখ্য কারণ বোধ করি এই, ‘পূজ্যপাদ পিতৃদেব শ্রীহৃষিকেশ শাস্ত্রী মহাশয়’ তাঁহার শুদ্ধিতত্ত্বের ৪৫ পৃষ্ঠায় মহামহোপাধ্যায় শ্রীকাশীরাম বাচস্পতির টীকার নকল করিয়া ‘অগ্নে’ লেখা সত্ত্বেও এই পদাঙ্কানুসারী বঙ্গীয় অনুবাদকটা ‘অগ্রে’ লিখিয়াছে! শুধু তাই নয়। আবার ‘অগ্নে’ শব্দটাকে প্রক্ষিপ্ত পর্যন্ত মনে করিয়াছে! সুতরাং এই অধ্যাপক ভট্টাচার্য মহাশয়ের নানাপ্রকার রসের উৎসব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। যথা—“স্তম্ভিত হইবেন, লজ্জায় ঘৃণায় অধোবদন হইবেন এবং যদি একবিন্দুও আর্যরক্ত আপনাদের ধমনীতে প্রবাহিত হয়, তবে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিবেন” ইত্যাদি ইত্যাদি। সব উচ্ছ্বাসগুলি লিখিতে গেলে সে অনেক স্থান এবং সময়ের আবশ্যক। সুতরাং তাহাতে কাজ নাই; যাঁহার অভিরুচি হয়, তিনি ভট্টাচার্য মহাশয়ের মূল প্রবন্ধে দেখিয়া লইবেন। তথাপি এ-সকল কথা আমি তুলিতাম না। কিন্তু এই দুটা কথা আমি সুস্পষ্ট করিয়া দেখাইতে চাই, আমাদের দেশের শাস্ত্রীর বিচার এবং শাস্ত্রীয় আলোচনা কিরূপ ব্যক্তিগত ও নিরর্থক উচ্ছ্বাসপূর্ণ হইয়া উঠে। এবং উৎকট গোঁড়ামি ধমনীর আর্যরক্তে এমন করিয়া তাণ্ডব নৃত্য বাধাইয়া দিলে মুখ দিয়া শুধু যে মান্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপভাষাই বাহির হয়, তাহা নয়, এমন সব যুক্তি বাহির হয়, যাহা শাস্ত্রীয় বিচারেই বল, আর যে-কোন বিচারেই বল, কোন কাজেই লাগে না। কিন্তু স্বর্গীয় দত্ত মহাশয়ের অপরাধটা কি? পণ্ডিতের পদাঙ্ক ত পণ্ডিতেই অনুসরণ করিয়া থাকে। সে কি মারাত্মক অপরাধ? পাশ্চাত্য পণ্ডিত কি পণ্ডিত নন যে, তাঁহার মতানুযায়ী হইলেই গালিগালাজ খাইতে হইবে!
দ্বিতীয় বিবাদ ঋক্বেদের ‘অগ্নে’ শব্দ লইয়া। এই পদাঙ্কানুসারী লোকটা কেন যে জানিয়া শুনিয়াও এ শব্দটাকে প্রক্ষিপ্ত মনে করিয়া ‘অগ্রে’ পাঠ গ্রহণ করিয়াছিল, সে আলোচনা পরে হইবে। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কি জানা নাই যে, বাংলার অনেক পণ্ডিত আছেন যাঁহারা পাশ্চাত্য পণ্ডিতের পদাঙ্ক অনুসরণ না করিয়াও অনেক প্রামাণ্য শাস্ত্রগ্রন্থের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, এবং তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কারণ, বুদ্ধিপূর্বক নিরপেক্ষ আলোচনার দ্বারা যদি কোন শাস্ত্রীয় শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়, তাহা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া বলাই ত শাস্ত্রের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা।
জ্ঞানতঃ চাপাচুপি দিয়া রাখা বা অজ্ঞানতঃ প্রত্যেক অনুস্বার বিসর্গটিকে পর্যন্ত নির্বিচারে সত্য বলিয়া প্রচার করায় কোন পৌরুষ নাই। তাহাতে শাস্ত্রেরও মান্য বাড়ে না, ধর্মকেও খাটো করা হয়। বরঞ্চ, যাহাদের শাস্ত্রের প্রতি বিশ্বাসের দৃঢ়তা নাই, শুধু তাহাদেরই এই ভয় হয়, পাছে দুই-একটা কথাও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধরা পড়িলে সমস্ত বস্তুটাই ঝুটা হইয়া ছায়াবাজির মত মিলাইয়া যায়। সুতরাং যাহা কিছু সংস্কৃত শ্লোকের আকারে ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার সমস্তটাই হিন্দুশাস্ত্র বলিয়া মানা চাই-ই।
বস্তুতঃ, এই সত্য ও স্বাধীন বিচার হইতে ভ্রষ্ট হইয়াই হিন্দুর শাস্ত্ররাশি এমন অধঃপাতিত হইয়াছে। নিছক নিজের বা দলটির সুবিধার জন্য কত যে রাশি রাশি মিথ্যা উপন্যাস রচিত এবং অনুপ্রবিষ্ট হইয়া হিন্দুর শাস্ত্র ও সমাজকে ভারাক্রান্ত করিয়াছে, কত অসত্য যে বেনামীতে প্রাচীনতার ছাপ মাখিয়া ভগবানের অনুশাসন বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তাহার সীমা-পরিসীমা নাই। জিজ্ঞাসা করি, ইহাকে মান্য করাও কি হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা করা? একটা দৃষ্টান্ত দিয়া বলি। কুলার্ণবের “আমিষাসবসৌরভ্যহীনং যস্য মুখং ভবেৎ। প্রায়শ্চিত্তী স বর্জ্জ্যাশ্চ পশুরেব ন সংশয়ঃ” ইহাও হিন্দুর শাস্ত্র! এ কথাও ভগবান মহাদেব বলিয়া দিয়াছেন! চব্বিশ ঘণ্টা মুখে মদ-মাংসের সুগন্ধ না থাকিলে সে একটা অন্ত্যজ জানোয়ারের সামিল। অধিকারিভেদে এই শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের দ্বারাও হিন্দু স্বর্গের আশা করে! কিন্তু তান্ত্রিকই হউক, আর যাই হউক, সে হিন্দু ত বটে! ইহা শাস্ত্রীয় বিধি ত বটে! সুতরাং স্বর্গবাসও ত সুনিশ্চিত বটে! কিন্তু, তবুও যদি কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত humbug বলিয়া হাসিয়া উঠেন, তাঁহার হাসি থামাইবারও ত কোন সদুপায় দেখিতে পাওয়া যায় না।
অথচ হিন্দুর ঘরে জন্মিয়া শ্লোকটিকে মিথ্যা বলাতেও শঙ্কা আছে। কারণ, আর দশটা হিন্দু-শাস্ত্র হইতে বচন বাহির হইয়া পড়িবে যে, মহেশ্বরের তৈরি এই শ্লোকটিকে যদি কেহ সন্দেহ করে, তাহা হইলে সে ত সে, তাহার ৫৬ পুরুষ নরকে যাইবে। আমাদের হিন্দুশাস্ত্র ত সচরাচর একপুরুষ লইয়া বড়-একটা কথা কহে না।
শ্রীভববিভূতি ভট্টাচার্য এম. এ. মহোদয় তাঁহার ‘চাতুর্ব্বণ্য ও আচার’ প্রবন্ধের গোড়াতেই চাতুর্ব্বণ্য সম্বন্ধে বলিতেছেন,—“যে চাতুর্ব্বণ্য প্রথা হিন্দু জাতির একটি মহৎ বিশেষত্ব, যাহা পৃথিবীর অন্য কোনও জাতিতে দৃষ্ট হয় না—যে সনাতন সুপ্রথা শান্তি ও সুশৃঙ্খলার সহিত সমাজ পরিচালনার একমাত্র সুন্দর উপায়,—যাহাকে কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ও তাঁহাদের পদাঙ্কানুসারী দেশীয় বিদ্বান্গণ হিন্দুর প্রধান ভ্রম এবং তাঁহাদের অধঃপতনের মূল কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন,—সেই চাতুর্ব্বর্ণ্য কত প্রাচীন, তাহা জানিতে হইলে বেদপাঠ তাহার অন্যতম সহায়।”
এই চাতুর্ব্বণ্য প্রসঙ্গে শুধু যদি ইনি লিখিতেন—এই কথা কত প্রাচীন, তাহা জানিতে হইলে বেদপাঠ তাহার অন্যতম সহায়, তাহা হইলে কোন কথা ছিল না; কারণ, উক্ত প্রবন্ধে বলিবার বিষয়ই এই। কিন্তু ঐ যে-সব আনুষঙ্গিক বক্র কটাক্ষ, তাহার সার্থকতা কোনখানে? “যে সনাতন সুপ্রথা শান্তি ও সমাজ-পরিচালনার একমাত্র সুন্দর উপায়—” জিজ্ঞাসা করি, কেন? কে বলিয়াছে? ইহা যে ‘সুপ্রথা’ তাহার প্রমাণ কোথায়? যে-কোন একটা প্রথা শুধু পুরাতন হইলেই ‘সু’ হয় না। ফিজিয়ানরা যদি জবাব দেয়, “মশাই, বুড়া বাপ-মাকে জ্যান্ত পুঁতিয়া ফ্যালার নিয়ম যে আমাদের দেশের কত প্রাচীন, সে যদি একবার জানিতে ত আর আমাদের দোষ দিতে না।”
সুতরাং এই যুক্তিতে ত ঘাড় হেঁট করিয়া আমাদিগকে বলিতে হইবে, “হাঁ বাপু, তোমার কথাটা সঙ্গত বটে! এ-প্রথা যখন এতই প্রাচীন, তখন আর ত কোন দোষ নাই। তোমাকে নিষেধ করিয়া অন্যায় করিয়াছি—বেশ করিয়া জ্যান্ত কবর দাও—এমন সুবন্দোবস্ত আর হইতেই পারে না!” অতএব শুধু প্রাচীনত্বই কোন বস্তুর ভাল-মন্দর সাফাই নয়। তবে এই যে বলা হইয়াছে যে, এই প্রথা কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রবর্তিত নহে, ইহা সেই পরমপুরুষের একটি ‘অঙ্গবিলাস’ মাত্র, তাহা হইলে আর কথা চলে না। কিন্তু আমার কথা চলুক আর না-চলুক, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না; কিন্তু যাহাতে যথার্থই আসিয়া যায়, অন্ততঃ আসিয়া গিয়াছে, তাহা এই যে, সেই সমস্ত প্রাচীন দিনের ঋষিদিগের অপরিমেয় অতুল্য বুদ্ধিরাশির ভরা-নৌকা এইখানেই ঘা খাইয়া চিরদিনের মত ডুবিয়াছে। যে-কেহ হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিয়াছেন, তিনিই বোধ করি অত্যন্ত ব্যথার সহিত অনুভব করিয়াছেন, কি করিয়া ঋষিদিগের স্বাধীন চিন্তার শৃঙ্খল এই বেদেরই তীক্ষ্ণ খড়্গে ছিন্নভিন্ন হইয়া পথে-বিপথে যেখানে-সেখানে যেমন-তেমন করিয়া আজ পড়িয়া আছে। চোখ মেলিলেই দেখা যায়, যখনই সেই সমস্ত বিপুল চিন্তার ধারা সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া ছুটিতে গিয়াছে, তখনই বেদ তাহার দুই হাত বাড়াইয়া তাহাদের চুলের মুঠি ধরিয়া টানিয়া আর একদিকে ফিরাইয়া দিয়াছে। তাহাদিগকে ফিরাইয়াছে সত্য, কিন্তু পাশ্চাত্য পণ্ডিত বা তাঁহাদেরই পদাঙ্কানুসারী দেশীয় বিদ্বান্গণকে ঠিক তেমন করিয়া নিবৃত্ত করা শক্ত।
কিন্তু সে যাই হউক, কেন যে তাঁহারা এই প্রথমটিকে হিন্দুর ভ্রম এবং অধঃপতনের হেতু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, অধ্যাপক মহাশয় তাহার যখন কিছুমাত্র হেতুর উল্লেখ না করিয়া শুধু উক্তিটা তুলিয়া দিয়াই ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছেন, তখন ইহা লইয়া আলোচনা করিবার আপাততঃ প্রয়োজন অনুভব করি না।
অতঃপর অধ্যাপক মহাশয় বলেন বৈদেশিক পণ্ডিতেরা পরমপুরুষের এই চাতুর্ব্বণ্য অঙ্গবিলাসটি মানিতে চাহেন না এবং বলেন, ঋক্বেদের সময়ে চাতুর্বর্ণ্য ছিল না। কারণ, এই বেদের আদ্য কতিপয় মণ্ডলে ভারতবাসিগণের কেবল দ্বিবিধ ভেদের উল্লেখ আছে। আর যদিই বা কোনস্থানে চাতুর্বর্ণ্যের উল্লেখ থাকে, তবে তাহা প্রক্ষিপ্ত।
এই কথায় অধ্যাপক মহাশয় ইহাদিগকে অন্ধ বলিয়া ক্রোধে ইহাদের চোখে আঙুল দিয়া দিবেন বলিয়া শাসাইয়াছেন। কারণ, আর্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, চতুর্বিধ ভেদের স্পষ্ট উল্লেখ থাকিতেও তাহা তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।
তার পর ‘আর্য্যং বর্ণং’ শব্দটার অর্থ লইয়া উভয় পক্ষের যৎকিঞ্চিৎ বচসা আছে। কিন্তু আমরা ত বেদ জানি না, সুতরাং এই ‘আর্য্যং বর্ণং’ শেষে কি মানে হইল, ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।
তবে মোটামুটি বুঝা গেল যে, এই ‘ব্রাহ্মণ’ শব্দটা লইয়া একটু গোল আছে। কারণ, ‘ব্রহ্ম’ শব্দটির ‘মন্ত্র’ অর্থও নাকি হয়!
অধ্যাপক মহাশয় বলিতেছেন, ম্যাক্সমুলারের এত সাহস হয় নাই যে বলেন, ‘ছিলই না’, কিন্তু প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, হিন্দু চাতুর্বর্ণ্য বৈদিক যুগে ‘স্পষ্টতঃ বিদ্যমান ছিল না’; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের যে বিভিন্ন বৃত্তির কথা শুনা যায়—তাহার তত বাঁধাবাঁধি বর্ণচতুষ্টয়ের মধ্যে তৎকালে আবির্ভূত হয় নাই—অর্থাৎ যোগ্যতা-অনুসারে যে-কোন লোক যে-কোন বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারিত।
আমার ত মনে হয়, পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার জোর করিয়া ‘ছিলই না’ না বলিয়া নিজের যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাতেই শুধু অর্জিত হয়। কিন্তু প্রত্যুত্তরে ভববিভূতিবাবু বলিতেছেন,—“সায়ণ চতুর্দশ শতাব্দীর লোক বলিয়া না হয় তাঁহার ব্যাখ্যা উড়াইয়া দিতে প্রবৃত্ত হইতে পার, কিন্তু সেই অপৌরুষেয় বেদেরই অন্তর্গত ঐতরেয় ব্রাহ্মণ যখন ‘ব্রহ্মণস্পতি’ অর্থে ব্রাহ্মণপুরোহিত। [ ঐ. ব্রা. ৮। ৫। ২৪, ২৬ ] করিলেন, তখন তাহা কি বলিয়া উড়াইয়া দিবে? ব্রহ্মণ্যশক্তি যে সমাজ ও রাজশক্তির নিয়ন্ত্রী ছিল, তাহা আমরা ঋগ্বেদেই দেখিতে পাই!”
পাওয়াই ত উচিত। কিন্তু কে উড়াইয়া দিতেছে এবং দিবার প্রয়োজনই বা কি হইয়াছে, তাহা ত বুঝা গেল না! ব্রাহ্মণ পুরোহিত—বেশ ত! পুরোহিতের কাজ যিনি করিতেন, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা হইত। যজন-যাজন করিলে ব্রাহ্মণ বলিত; যুদ্ধ, রাজ্য-পালন করিলে ক্ষত্রিয় বলিত—এ কথা ত তাঁহারা কোথাও অস্বীকার করেন নাই। আদালতে বসিয়া যাঁহারা বিচার করেন, তাঁহাদিগকে জজ বলে, উকিল বলে না। শ্রীযুক্ত গুরুদাসবাবু যখন ওকালতি করিতেন, তাঁহাকে লোকে উকিল বলিত, জজ হইলে জজ বলিত।
ইহাতে আশ্চর্য হইবার আছে কি? ব্রাহ্মণ্যশক্তি বৈদিক যুগে রাজশক্তির নিয়ন্ত্রী ছিল। ইংরাজের আমলে বড়লাট ও মেম্বারেরা তাহাই, সুতরাং এই মেম্বারেরা রাজশক্তির নিয়ন্ত্রী ছিল বলিয়া একটা কথা যদি ভারতবর্ষের ইংরাজী ইতিহাসে পাওয়া যায় ত তাহাতে বিস্মিত হইবার বা তর্ক করিবার আছে কি? অথচ লাটের ছেলেরা লাটও হয় না, মেম্বার বলিয়াও কোন স্বতন্ত্র জাতির অস্তিত্ব নাই। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের প্রাচীনতা সম্বন্ধে শুনিতে পাই, নানাপ্রকার মতভেদ আছে। এই সম্পর্কে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার একটি অতিবড় অপকর্ম করিয়াছেন—তিনি লিখিয়াছেন—“কবষ শূদ্র হইয়াও দশম মণ্ডলের অনেকগুলি মন্ত্রের প্রণেতা (?)।”
‘দ্রষ্টা’ বলা তাঁহার উচিত ছিল। এই হেতু ভববিভূতিবাবু ক্ষুব্ধ ও বিস্মিত হইয়া (?) চিহ্ন ব্যবহার করিয়াছেন।
কিন্তু আমি বলি, বিদেশীর সম্বন্ধে অত খুঁটিনাটি ধরিতে নাই। কারণ, এই দশম মণ্ডলেরই ৮৫ সূক্তে সোম ও সূর্যের বিবাহ বর্ণনা করিয়া তিনি নিজেই বলিয়াছেন, এমন পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে আকাশের গ্রহ-তারার সম্বন্ধ বাঁধিবার চেষ্টা জগতের আর কোন সাহিত্যে দেখা যায় কি? এমন চেষ্টা জগতের আর কোন সাহিত্যে দেখা না যাইতে পারে; কিন্তু কোন একটা উদ্দেশ্য সাধন করিবার অভিপ্রায় বৈদিক কবিকে যে শ্লোকটি বিশেষ করিয়া সৃষ্টি করিতে হইয়াছিল, তাহাকে বিদেশীয় কেহ যদি সেই কবির রচিত বলিয়া মনে করে, তাহাতে রাগ করিতে আছে কি? কিন্তু সে যাই হোক, সূক্তটি যে রূপকমাত্র, তাহা ভববিভূতিবাবু নিজেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। সুতরাং, স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, অপৌরুষেয় বেদের অন্তর্গত সূক্তরাশির মধ্যেও এমন সূক্ত রহিয়াছে, যাহা রূপকমাত্র, অতএব খাঁটি সত্য হইতে বাছিয়া ফেলা অত্যাবশ্যক। এই অত্যাবশ্যক কাজটি যাহাকে দিয়া করাইতে হইবে, সে বস্তু কিন্তু বিশ্বাসপরায়ণতা বা ভক্তি নহে—সে মানুষের সংশয় এবং তর্কবুদ্ধি! অতএব ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তাহাকেই সকলের উপর স্থান দান করিতেই হইবে। না করিলে মানুষ মানুষই হইতে পারে না। কিন্তু, এই মনুষ্যত্ব চিরদিন সমভাবে থাকে না—সেইজন্য ইহাও কল্পনা করা অসম্ভব নয় যে, হয়ত এই ভারতেই একদিন ছিল, যখন এই চন্দ্র ও সূর্যের বিবাহ-ব্যাপারটা খাঁটি সত্য ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিতে মানুষ ইতস্ততঃ করে নাই। আবার আজ যাহাকে সত্য বলিয়া আমরা অসংশয়ে বিশ্বাস করিতেছি, তাহাকেই হয়ত আমাদের বংশধরেরা রূপক বলিয়া উড়াইয়া দিবে! আজ আমরা জানি, সূর্য এবং চন্দ্র কি বস্তু এবং এইরূপ বিবাহ-ব্যাপারটাও কিরূপ অসম্ভব; তাই ইহাকে রূপক বলিতেছি। কিন্তু এই সূক্তই যদি আজ কোন পল্লীবাসিনী বৃদ্ধা নারীর কাছে বিবৃত করিয়া বলি, তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা করিবেন না। কিন্তু তাহাতে কি বেদের মাহাত্ম্য বৃদ্ধি করিবে? ভববিভূতিবাবু ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯০ সূক্ত উদ্ধৃত করিতে গিয়া কঠিন হইয়া বলিতেছেন,—“ইহাতেও কাহারও সন্দেহ থাকিলে তাহার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দশম মণ্ডলের ৯০ সূক্ত বা প্রখ্যাত ‘পুরুষসূক্তের’ দ্বাদশ ঋক্টি দেখাইয়া দিব, যথা—
ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরু তদস্য যদ্বৈস্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত।।
অর্থ—সেই পরমপুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে রাজন্য বা ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্র উৎপন্ন হইল। ইহার অপেক্ষা চাতুর্ব্বর্ণ্যের আর স্পষ্ট উল্লেখ কি হইতে পারে?”
এই সূক্তটির বিচার পরে হইবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের উদ্দেশ্য ভববিভূতিবাবু যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। ইনি বলিতেছেন যে, “আমাদের চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রথার অর্ব্বাচীনতা প্রতিপন্ন করিয়া আমাদের ভারতীয় সভ্যতাকে আধুনিকরূপে জগৎসমক্ষে প্রচার করা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের প্রধান উদ্দেশ্য হইতে পারে এবং সেই উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া ইত্যাদি—”
এরূপ উদ্দেশ্যকে সকলেই নিন্দা করিবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সমস্ত উদ্দেশ্যেরই একটা অর্থ থাকে। এখানে অর্থটা কি? একটা সত্য বস্তুর কদর্থ বা কু-অর্থ করার হেয় উপায় অবলম্বন করিয়া চাতুর্বর্ণ্যকে বৈদিক যুগ হইতে নির্বাসিত করিয়া তাহাকে অপেক্ষাকৃত আধুনিক প্রতিপন্ন করায় এই পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের লাভটা কি? শুধু চাতুর্বর্ণ্যই কি সভ্যতা? ইহাই কি বেদের সর্বপ্রধান রত্ন? চাতুর্বর্ণ্য বৈদিক যুগে থাকার প্রমাণ আমরা দাখিল না করিতে পারিলেই কি জগৎসমক্ষে প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে যে, আমাদের পিতামহেরা বৈদিক যুগে অসভ্য ছিল? পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মিশর, বেবিলন প্রভৃতি দেশের সভ্যতা ৮।১০ হাজার বৎসর পূর্বের বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের বেলাই তাঁহাদের এতটা নীচতা প্রকাশ করিবার হেতু কি?
তা ছাড়া, অধ্যাপক ম্যাক্সমুলার ঋক্বেদের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহার সহিত ভববিভূতিবাবুর এই মন্তব্য খাপ খায় না। আমার ঠিক স্মরণ হইতেছে না (এবং বইখানাও হাতের কাছে নাই), কিন্তু মনে যেন পড়িতেছে, তিনি Kant-এর Critique of the Pure Reason-এর ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—জগতে আসিয়া যদি কিছু শিখিয়া থাকি ত সে ঋক্বেদ ও এই Critique হইতে। একটা গ্রন্থের ভূমিকায় আর একটা গ্রন্থের উল্লেখ এমন অযাচিতভাবে করা সহজ শ্রদ্ধার কথা নয়।
তবে যে কেন তিনি ইহাকেই খাটো করিয়া দিবার প্রয়াস করিয়া আশাতীত সঙ্কীর্ণ অন্তঃকরণের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভববিভূতিবাবু বলিতে পারেন। যাই হউক, এই ‘হিন্দুজাতির প্রাণস্বরূপ’ ১০ম মণ্ডলের ৯০ সূক্তটি অপৌরুষেয় ঋক্বেদেরই অন্তর্গত থাকা সত্ত্বেও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের পদাঙ্কানুসারী বঙ্গীয় অনুবাদক তাহাকে প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করায় ভববিভূতি মহাশয় “বড়ই কাতরকণ্ঠে দেশের আশা-ভরসাস্থল ছাত্রবৃন্দ ব্রাহ্মণতনয়গণ” কে ডাকাডাকি করিতেছেন, সেই সূক্তটি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহাকেও ডাক দেওয়া উচিত নয়। ইতিপূর্বেই এই ১০ম মণ্ডলেরই ৮৫ সূক্ত সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া গিয়াছে; তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রখ্যাত ৯০ সূক্তটি কি? ইহা পরমপুরুষের মুখ-হাত-পা দিয়া ব্রাহ্মণ প্রভৃতির তৈরী হওয়ার কথা।
কিন্তু ইহা জটাপাঠ, পদপাঠ, শাকল, বাস্কল দিয়া যতই যাচাই হইয়া গিয়া থাকুক না কেন, বিশ্বাস করিতে হইলে অন্ততঃ আরও শ-চারেক বৎসর পিছাইয়া যাওয়া আবশ্যক। কিন্তু সে যখন সম্ভব নহে, তখন আধুনিক কালে সংসারের চৌদ্দ আনা শিক্ষিত সভ্য লোক যাহা বিশ্বাস করেন—সেই অভিব্যক্তির পর্যায়েই মানুষের জন্ম হইয়াছে বলিয়া মানিতে হইবে। তার পর কোটি কোটি বৎসর নানাভাবে তাহার দিন কাটিয়া, শুধু কাল, না হয় পরশু সে সভ্যতার মুখ দেখিয়াছে। এ-পৃথিবীর উপর মানবজন্মের তুলনায় চাতুর্বর্ণ্য ঋগ্বেদে থাকুক আর না-থাকুক, সে কালকের কথা। অতএব হিন্দুজাতির প্রাণস্বরূপ এই সূক্তটিতে চাতুর্বর্ণ্যের সৃষ্টি যেভাবে দৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা প্রক্ষিপ্ত না হইলেও খাঁটি সত্য জিনিস নয়—রূপক।
কিন্তু ভয়ানক মিথ্যা, তদপেক্ষা ভয়ানক সত্য-মিথ্যায় মিশাইয়া দেওয়া। কারণ, ইহাতে না পারা যায় সহজে মিথ্যাকে বর্জন করা, না যায় নিষ্কলঙ্ক সত্যকে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধায় গ্রহণ করা। অতএব, এই রূপকের মধ্য হইতে নীর ত্যজিয়া ক্ষীর শোষণ করা বুদ্ধির কাজ। সেই বুদ্ধির তারতম্য অনুসারে একজন যদি ইহার প্রতি অক্ষরটিকে অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে করে এবং আর একজন সমস্ত সূক্তটিকে মিথ্যা বলিয়া ত্যাগ করিতে উদ্যত হয়, তখন অপৌরুষেয়ের দোহাই দিয়া তাহাকে ঠেকাইবে কি করিয়া? সে যদি কহিতে থাকে, ইহাতে ব্রাহ্মণের ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, বৈশ্যের ধর্ম, শূদ্রের ধর্ম—এই চারি প্রকার নির্দেশ করা হইয়াছে, জাতি বা মানুষ নয় অর্থাৎ সেই পরমপুরুষের মুখ হইতে যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা প্রভৃতি এক শ্রেণীর বৃত্তি; তাহাকে ব্রহ্মণ্যধর্ম বা ব্রাহ্মণ বলিবে। হাত হইতে ক্ষত্রিয়—অর্থাৎ বল বা শক্তির ধর্ম। এই প্রকার অর্থ যদি কেহ গ্রহণ করিতে চাহে, তাহাকে ‘না’ বলিয়া উড়াইয়া দিবে কি করিয়া? কিন্তু এইখানে একটা প্রশ্ন করিতে চাহি। এই যে এতক্ষণ ধরিয়া ঠোকাঠুকি কাটাকাটি করিয়া কথার শ্রাদ্ধ হইয়া গেল, তাহা কাহার কি কাজে আসিল? মনের অগোচর ত পাপ নাই? কতকটা বিদ্যা প্রকাশ করা ভিন্ন কোন পক্ষের আর কোন কাজ হইল কি? পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যদি বলিয়াইছিলেন, চাতুর্ব্বণ্য হিন্দুর বিরাট ভ্রম এবং অধঃপতনের অন্যতম কারণ এবং ইহা ঋক্বেদের সময়েও ছিল না—তবে ভববিভূতিবাবু যদি প্রতিবাদই করিলেন, তবে শুধু গায়ের জোরে তাঁদের কথাগুলা উড়াইয়া দিবার ব্যর্থ চেষ্টা না করিয়া কেন প্রমাণ করিয়া দিলেন না, এ প্রথা বেদে আছে। কারণ, বেদ অপৌরুষেয়, তাহার ভুল হইতে পারে না—জাতিভেদ প্রথা সুশৃঙ্খলার সহিত সমাজ-পরিচালনের যে সত্য সত্যই একমাত্র উপায়, তাহা এই সব বৈজ্ঞানিক, সামাজিক এবং ঐতিহাসিক নজির তুলিয়া দিয়া প্রমাণ করিয়া দিলাম।
তবে ত তাল ঠুকিয়া বলা যাইতে পারিত, এই দেখ, আমাদের অপৌরুষেয় বেদে যাহা আছে, তাহা মিথ্যাও নয় এবং তাহাকে অবলম্বন করিয়া হিন্দু ভুলও করে নাই, অধঃপথেও যায় নাই। তা যদি না করিলেন, তবে তাঁহারা জাতিভেদকে ভ্রমই বলুন আর যাই বলুন, সে-কথার উল্লেখ করিয়া শুধু শ্লোকের নজির তুলিয়া উহাদিগকে কানা বলিয়া, সঙ্কীর্ণচেতা বলিয়া, আর রাশি রাশি হা-হুতাশ উচ্ছ্বাসের প্রবাহ বহাইয়া দিয়াই কি কোন কাজ হইবে? বেদের মধ্যে যখন রূপকের স্থান রহিয়াছে, তখন বুদ্ধি-বিচারের অবকাশ আছে। সুতরাং শুধু উক্তিকেই অকাট্য যুক্তি বলিয়া দাঁড় করানো যাইবে না। আমি এই কথাটাই আমার এই ভূমিকায় বলিতে চাহিয়াছি।
অতঃপর হিন্দুর সর্বশ্রেষ্ঠ সংস্কার বিবাহের কথা। ইনি প্রথমেই বলিতেছেন, “হিন্দুর এই পবিত্র বিবাহপদ্ধতি বহু সহস্র বৎসর পূর্বে,—ঋগ্বেদের সময়ে যেভাবে নিষ্পন্ন হইত, আজও—একালের বৈদেশিক সভ্যতার সংঘর্ষেও তাহা অণুমাত্র পরিবর্তিত হয় নাই।” অণুমাত্রও পরিবর্তিত যে হয় নাই, তাহা নিম্নলিখিত উদাহরণে সুস্পষ্ট করিয়াছেন—
“তখনও বরকে কন্যার গৃহে গিয়া বিবাহ করিতে হইত,—এখনও তাহা হইয়া থাকে। আবার বিবাহের পর শোভাযাত্রা করিয়া, বহুবিধ অলঙ্কারভূষিতা কন্যাকে লইয়া শ্বশুর-দত্ত নানাবিধ যৌতুক সহিত তখনও যেমন বর গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন, এখনও সেইরূপ হইয়া থাকে। বিবাহযোগ্যকালে কন্যা-সম্প্রদানের ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু ঐ বয়সের কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট নাই। কন্যা শ্বশুরালয়ে আসিয়া কর্ত্রীর স্থান অধিকার করিতেন, এবং শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর ও ননদগণের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিতেন অর্থাৎ সকলকে বশ করিতেন।”
অতঃপর এই সকল উক্তি সপ্রমাণ করিতে নানাবিধ শ্লোক ও তাহার মন্তব্য লিখিয়া দিয়া বোধ করি অসংশয়ে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, এই সকল আচার-ব্যবহার বৈদিক কালে প্রচলিত ছিলই। ভালই।
কিন্তু এই যে বলিয়াছেন—বহু সহস্র বর্ষ পূর্বের বিবাহপদ্ধতি যেমনটি ছিল, আজও এই বৈদেশিক সভ্যতার সংঘর্ষেও ঠিক তেমনটি আছে, ‘অণুমাত্র’ পরিবর্তিত হয় নাই—ইহার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম না। কারণ, পরিবর্তিত না হওয়ায় বলিতেই হইবে, আজকাল প্রচলিত বিবাহপদ্ধতিটিও ঠিক তেমনি নির্দোষ এবং ইহাই বোধ করি বলার তাৎপর্য। কিন্তু এই তাৎপর্যটির সামঞ্জস্য রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে না। বলিতেছেন,—“কন্যা-সম্প্রদানের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু কন্যার বয়সের কোন পরিমাণ নির্দিষ্ট নাই।”
অর্থাৎ বুঝা যাইতেছে, আজকাল যেমন মেয়ের বয়স বারো উত্তীর্ণ হইয়া তেরোয় পড়িলেই ভয়ে এবং ভাবনায় মেয়ের বাপ-মায়ের জীবন দুর্ভর হইয়া উঠে এবং পাছে চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ এবং সমাজে ‘একঘরে’ হইয়া থাকিতে হয়, সেই ভয় ও ভাবনায় বাড়িসুদ্ধ লোকের পেটের ভাত চাল হইতে থাকে, তখনকার বৈদিক কালে এমনটি হইতে পারিত না। ইচ্ছামত বা সুবিধামত মেয়েকে ১২। ১৪। ১৮। ২০ যে-কোন বয়সেই হউক, পাত্রস্থ করা যাইতে পারিত। আর এমন না হইলে কন্যা শ্বশুরবাড়ি গিয়াই যে শ্বশুর-শাশুড়ি, ননদ-দেবরের উপর প্রভু হইয়া বসিয়া যাইত, সে নেহাত কচি খুকীটির কর্ম নয় ত।
রাগ দ্বেষ অভিমান গৃহিণীপনার ইচ্ছা প্রভৃতি যে সেকালে ছিল না—বউ বাড়ি ঢুকিবামাত্রই তাঁহার হাতে লোহার সিন্দুকের চাবিটি শাশুড়ী ননদে তুলিয়া দিত, সেও ত মনে করা যায় না।
যাই হউক, ভববিভূতিবাবুর নিজের কথা মত বয়সের কড়াকড়ি তখন ছিল না। কিন্তু এখন কড়াকড়িটা যে কি ব্যাপার, তাহা আর কোন ব্যক্তিকেই বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যকতা নাই বোধ করি।
দ্বিতীয়ঃ, ইনি বলিয়াছেন যে, “এই সকল উপঢৌকন কেহ যেন বর্তমানকালে প্রচলিত কদর্য পণপ্রথার প্রমাণরূপে গ্রহণ না করেন। এগুলি কন্যার পিতার স্বেচ্ছাকৃত, সামর্থ্যানুরূপ দান বুঝিতে হইবে।”
কিন্তু এখনকার উপঢৌকন যোগাইতে অনেক পিতাকে বাস্তুভিটাটি পর্যন্ত বেচিতে হয়। সে সময় কিন্তু অপৌরুষেয় ঋক্মন্ত্র মেয়ের বাপেরও এক তিল কাজে আসে না, বরের বাপকেও বিন্দুমাত্র ভয় দেখাইতে, তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না।
তৃতীয়তঃ, রাশীকৃত শাস্ত্রীয় বিচার করিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, যে-মেয়ের ভাই ছিল না, সে মেয়ের সহিত তখনকার দিনে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। এবং বলিতেছেন, অথচ, আজকাল এই বিবাহই সর্বাপেক্ষা সন্তোষজনক। কারণ, বিষয়-আশয় পাওয়া যায়। যদিচ, এতগুলি শাস্ত্রীয় শ্লোক ও তাহার অর্থাদি দেওয়া সত্ত্বেও মোটাবুদ্ধিতে আসিল না, ভাই না হওয়ায় বোনের অপরাধ কি এবং কেনই বা সে ত্যাজ্যা হইয়াছিল; কিন্তু এখন যখন ইহাই সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, তখন ইহাকেও একটা পরিবর্তন বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে। তবেই দেখা যাইতেছে,
(১) তখন মেয়ের বিবাহের বয়স নির্দিষ্ট ছিল না, এখন ইহাই হইয়াছে বাপ-মায়ের মৃত্যুবাণ।
(২) স্বেচ্ছাকৃত উপঢৌকন দাঁড়াইয়াছে বাস্তুভিটা বেচা এবং
(৩) নিষিদ্ধ কন্যা হইয়াছেন সবচেয়ে সুসিদ্ধ মেয়ে।
ভববিভূতিবাবু বলিবেন, তা হোক না, কিন্তু এখনও ত বরকে সেই মেয়ের বাড়িতে গিয়াই বিবাহ করিতে হয় এবং শোভাযাত্রা করিয়া ঘরে ফিরিতে হয়। এ ত আর বৈদেশিক সভ্যতার সংঘর্ষ একতিল পরিবর্তিত করিতে পারে নাই? তা পারে নাই সত্য, তবুও মনে পড়ে, সেই যে কে একজন খুব খুশী হইয়া বলিয়াছিল,—“অন্নবস্ত্রের দুঃখ ছাড়া আর দুঃখ আমার সংসারে নেই!”
আবার ইহাই সব নয়। “বিবাহিতা পত্নী যে গৃহের প্রধান অঙ্গ,—গৃহিণীর অভাবে যে গৃহ জীর্ণারণ্যের তুল্য”, তাহা ভট্টাচার্য্য মহাশয় “গৃহিণী গৃহমুচ্যতে”—এই প্রসিদ্ধ প্রবাদবাক্য হইতে সম্প্রতি অবগত হইয়াছেন। আবার ঋগ্বেদ পাঠেও এই প্রবাদটির সুপুরাতনত্বই সূচিত হইয়াছে। যথা—[৩ ম, ৫৩ সূ, ৪ ঋক্]
“জায়েদস্তং মঘবন্ত্ সেদু যোনিঃ”
অর্থাৎ হে মঘবন্—জায়াই গৃহ, জায়াই যোনি। সুতরাং বহু প্রাচীনকাল হইতেই হিন্দুগণ রমণীগণের প্রতি আদর ও সম্মান প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। আবার তাঁহাদের পত্নী কিরূপ মঙ্গলময়ী, তাহা “কল্যাণীর্জায়া … গৃহে তে” [৩ ম, ৫৩ সূ, ৬ ঋক্] হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয়। সুতরাং—
“কিন্তু তথাপি বৈদেশিকগণ কেন যে হিন্দুগণের উপর রমণীগণের প্রতি কঠোর ব্যবহারের জন্য দোষারোপ করেন, তাহা তাঁহারাই জানেন।”
এই সকল প্রবন্ধ ও মতামতের যে প্রতিবাদ করা আবশ্যক, সে কথা অবশ্য কেহই বলিবেন না। আমিও একেবারেই করিতাম না, যদি না ইহা আমার প্রবন্ধের ভূমিকা হিসাবেও কাজে লাগিত। তথাপি প্রতিবাদ করিতে আমি চাহি না — কিন্তু ইহারই মত ‘বড় কাতরকণ্ঠে’ ডাকিতে চাহি—ভগবন্! এই সমস্ত শ্লোক আওড়ানোর হাত হইতে এই হতভাগ্য দেশকে রেহাই দাও। ঢের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া লইয়াছ, এইবার একটু নিষ্কৃতি দাও। -শ্রীমতী অনিলা দেবী ( ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩)
সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (এক)
বাঙলার হিন্দু জনগণের আজকের এই সম্মিলনী যাঁরা আহ্বান করেছেন, আমি তাঁদের একজন। এই বিশাল সভা কেবলমাত্র এই নগরের নাগরিকগণের নয়। আজ যাঁরা সমবেত হয়েছেন, তাঁরা বাঙলার বিভিন্ন জেলার অধিবাসী। সকলের বর্ণ হয়ত এক নয়, কিন্তু ভাষা এক, সাহিত্য এক, ধর্ম এক, জীবনযাত্রার গোড়ার কথাটা এক,—যে বিশ্বাস যে নিষ্ঠা আমাদের ইহলোক পরলোক নিয়ন্ত্রিত করে, সেখানেও আমরা কেউ কারও পর নয়। পর করে দেবার নানা উপায়, নানা কৌশল সত্ত্বেও বলব, আমরা আজও এক। যুগ-যুগান্ত থেকে যে বন্ধন আমাদের এক করে রেখেছে, সত্যিই আজও তা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি।
বাঙলার সেই সমগ্র হিন্দু জাতির পক্ষ থেকে, যাঁরা এই সভার উদ্যোক্তা, তাঁদের পক্ষ থেকে আমি সবিনয়ে সসম্মানে রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করি—এই বিপুলায়তন সভার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে।
একটা প্রথা আছে সভাপতির পরিচয় দেওয়া; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই বিরাট নামের সম্মুখে পিছনে পরিচয়ের কোন্ বিশেষণ যোগ করা যায়? বিশ্বকবি, কবিসার্বভৌম ইত্যাদি অনেক কিছু মানুষে পূর্বেই আরোপ করে রেখেছে। কিন্তু আমরা—যাঁরা তাঁর শিষ্য-সেবক—নিজেদের মধ্যে শুধু ‘কবি’ বলেই তাঁর উল্লেখ করি।—বাইরে বলি রবীন্দ্রনাথ। জানি, সভ্যজগতের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত এই ব্যক্তিটিকে বোঝাবার পক্ষে কারও অসুবিধা ঘটবে না। কবির মন ক্লান্ত, দেহ দুর্বল, অবসন্ন। এই বিপুল জনতার মাঝখানে তাঁকে আহ্বান করে আনা বিপজ্জনক। তবু তাঁকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম। মনে মনে ইচ্ছে ছিল, দুনিয়ার কারও না অবিদিত থাকে এই সভার নেতৃত্বের ভার বহন করলেন কে? কবি স্বীকার করলেন, বললেন, ভাল, তাঁর বক্তব্য তাঁর নিজের মুখ দিয়েই তবে ব্যক্ত হোক।
তাঁকে আমাদের সকৃতজ্ঞ চিত্তের নমস্কার নিবেদন করি।
ভারত-রাজ্যশাসনের নূতন যন্ত্র বিলাতের মন্ত্রীগণ বহুদিনে বহু যত্নে প্রস্তুত করেছেন।
জাহাজে বোঝাই দেওয়া হয়েছে,—এলো বলে। তার ছোট-বড় কত চাকা, কত দণ্ড, কত কলকব্জা কোন্টা কোন্দিকে ঘোরে কোন্দিকে ফেরে কোন্ মুখে এগোয় আমার কেউ ঠিক জানিনে। এবং মূল্য তার শেষ পর্যন্ত যে কি দিতে হবে, সে ধারণাও কারো নেই।
যন্ত্র-নির্মাণের সময় মাঝে মাঝে শুধু খবর পাওয়া যেতো, এদেশ থেকে ওদেশে বহু বুদ্ধিমান চালান দেওয়া হয়েছে, বুদ্ধি দেবার জন্যে। কি বুদ্ধি তাঁরা দিলেন, সে সূক্ষ্ম তত্ত্ব আমরা সাধারণ মানুষে বুঝিনে, কেবল এইটুকু বোঝা গিয়েছিল, একপক্ষ তারস্বরে অনেক চীৎকার করেছিলেন, ও নূতন যন্ত্রে তাঁদের কাজ নেই এবং অপরপক্ষ ধমক দিয়ে বলেছিলেন, আলবত্ কাজ আছে—চেঁচিও না। অতএব কাজ আছে শেষ পর্যন্ত স্বীকার করতেই হলো। অনেকের ধারণা, সেটা নাকি মস্ত বড় আকমাড়া কলের মত। তার একদিকে জমা হবে ছিবড়ে, অন্য দিকে রস। শেষেরটা পাত্রে সঞ্চিত হয়ে কোন্দিকে চালান যাবে, সে প্রশ্ন শুধু বাহুল্য নয়, হয়ত বা অবৈধ। ভয় আছে। তথাপি প্রশ্ন করা চলে। রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মবিশ্বাসই কি হয়ে দাঁড়াল সকলের বড়? আর মানুষ হলো ছোট? যে ব্যবস্থা জগতের কোথাও নেই, কোথাও কল্যাণ হয়নি, এই দুর্ভাগা দেশে তাই কি হলো special and peculiar circumstances? আর সে কেউ বোঝে না—নাবালকের trusteeরা ছাড়া?
কিন্তু এ হলো politics, এ আলোচনা করবার ভার নেই আমার উপর। এ বিষয়ে যাঁরা ওয়াকিবহাল, তাঁরাই এ তত্ত্ব বুঝিয়ে দেবার যোগ্য পাত্র। আমি নয়।
তবুও পরিশেষে একটা কথা বলে রাখি। কারও কারও ধারণা—আমরা বিলেতে memorial পাঠিয়েছি সুবিচারের আশায়। সে বিশ্বাস আমাদের কারও নেই, আমরা পাঠিয়েছি অন্যায়ের প্রতিবাদ। নূতন শাসনব্যবস্থার আগাগোড়াই মন্দ। সেই অপরিসীম মন্দের মধ্যেও বাঙলায় হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হলো সবচেয়ে বেশী। আইনের পেরেক ঠুকে তাঁদের ছোট করা হলো চিরদিনের মত। তথাপি এ কথা সত্য যে, দেশের মুসলমান ভাইয়েরা দশ-পনেরটা স্থান বেশী পেয়েছেন বলে তাঁদের বলতে চাই,—অন্যায়, অবিচার—একজনের প্রতি হলেও সে অকল্যাণময়। তাতে শেষ পর্যন্ত না মুসলমানের, না হিন্দুর, না জন্মভূমির—কাহারও মঙ্গল হয় না।(‘ বাতায়ণ’ ১ শ্রাবণ, ১৩৪৩)
সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (দুই)
নূতন শাসনতন্ত্রে সমগ্র ভারতের হিন্দুদিগের, বিশেষতঃ বাঙলাদেশের হিন্দুদিগের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে—এত বড় অবিচার আর কিছুতে হতে পারে না। অনেকে হয়ত এই মনে করবেন যে, এই অবিচারের প্রতিকার করবার ক্ষমতা আমাদের হাতে নেই এবং এই মনে করেই তাঁরা নিশ্চেষ্ট থাকবেন, প্রতিবাদ করবেন না। কিন্তু তা সত্য নয়; যদি এই অন্যায়কে রোধ করবার ক্ষমতা কারও থাকে, সে আমাদেরই আছে।
নিজের শক্তিমত আমি আজন্মকাল সাহিত্যসেবা করে এসেছি,—যদি দেশের সাহিত্য বড় হয় এই আশায়;—এবং এই আশাতেই সাহিত্যের কাজে, দেশের কাজে, নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করেছি। কিন্তু এখন অবস্থা এমন হতে চলেছে যে, আমার ভয় হয়—হয়ত দশ বৎসরের মধ্যে সাহিত্যের আর এক যুগ এসে পড়বে;—হয়ত রবীন্দ্রনাথ সেদিন থাকবেন না, আমিও হয়ত ততদিন আর থাকব না। তাই এখন হতে সেই অবস্থার কথা ভেবে আমি শঙ্কিত হয়ে পড়েছি।
বাংলা-সাহিত্যকে বিকৃত করবার একটি হীন প্রচেষ্টা চলেছে। কেউ বলছেন, সংখ্যার অনুপাতে ভাষার মধ্যে এতগুলি ‘আরবী’ কথা ব্যবহার কর; কেউ বলছেন, এতগুলি ‘পারসী’ কথা ব্যবহার কর; আবার কেউ বা বলছেন, এতগুলি ‘উর্দু’ কথা ব্যবহার কর। এটা একেবারে অকারণ,—যেমন ছোট ছেলে হাতে ছুরি পেলে বাড়ির সমস্ত জিনিস কেটে বেড়ায়, এ-ও সেইরূপ।
তারপর এতবড় অবিচার যে আমাদের—হিন্দুদের উপর হলো, এ তাঁরা জেনেও নীরব হয়ে রইলেন—এইটাই সকলের চেয়ে দুঃখের কথা। এটা কি তাঁরা বোঝেন না যে, এই যে বিষ, এই যে ক্ষোভ হিন্দুদের মনের মধ্যে জমা হয়ে রইল—একদিন না একদিন তা রূপ পাবেই; তার যে একটি প্রতিক্রিয়া আছে, এও কি তাঁরা ভাবেন না? এরকম করে ত আর একটা দেশ চলতে পারে না, একটা জাতি বাঁচতে পারে না—এটাও ত তাঁদের জন্মভূমি। দেখুন, কেবল দিলেই হয় না,—গ্রহণ করার শক্তিও একটা শক্তি। আজ যদি তাঁরা মনে করেন যে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ঢেলে দিলেন বলেই তাঁদের পাওয়া হলো—একদিন টের পাবেন, এত বড় ভুল আর নেই।
আমি আমার মুসলমান ভায়েদের বলছি, তোমরা সংস্কৃতির উপর নজর রেখো, সাহিত্যের উপর নজর রেখো, আর ছোট ছেলের মত ধারালো ছুরি হাতে পেয়েছ বলে সব কেটে ফেলো না।
আমার মতে অন্যায় স্বীকার করতে নেই, যথাসাধ্য প্রতিকার করতে হয়; তাই দিয়েই মানুষ মানুষ হয়ে উঠে। এই যে অন্যায়টা আমাদের উপর হয়েছে, তার প্রতিকার করতেই হবে; যদি না পারি, তা হলে দশ বৎসর পরে—বাঙালী আজ যা নিয়ে গৌরব করছে—তার আর কিছুই থাকবে না। তাই আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে যতখানি পারি এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করবো; কারণ অন্যায় যদি চলতে দেওয়া হয়, তবে দেশে না হিন্দুর না মুসলমানের, না কারো কখন মঙ্গল হবে। (‘ বাতায়ণ’ ১৫ শ্রাবণ, ১৩৪৩)
সাহিত্য সম্মিলনের রূপ
সেদিন হুগলি জেলায় কোন্নগর গ্রামে এমনি এক সাহিত্যিক সম্মেলনে স্নেহাস্পদ লালমিঞা ভাই সাহেব আমাকে যখন আপনাদের ফরিদপুর শহরে আসার জন্যে আমন্ত্রণ করলেন, তখন সেই নিমন্ত্রণ আমি সানন্দে গ্রহণ করে এই অনুরোধ জানিয়েছিলাম, আমি যাবো সত্য কিন্তু এবার যেন এ আসরে বহু-আচরিত বহু-প্রচলিত গতানুগতিক প্রথার পরিবর্তন হয়। বলেছিলাম, তোমাদের ফরিদপুরের মিলনক্ষেত্রে এবার যেন সাহিত্যসেবী ও সাহিত্য-রস-পিপাসুগণের সম্যক্ মিলনের কার্যটা যথার্থভাবে সুসম্পন্ন হতে পায়; কাজের তাড়ায়, প্রবন্ধের ভিড়ে, সু ও কু-সাহিত্যের সংখ্যা নিরূপণের বাগ্-বিতণ্ডায় এর আবহাওয়া যেন ঘুলিয়ে উঠতে না পারে।
বছরে বছরে বঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হয় কখনো বা বাঙলার বাহিরে কখনো বা ভিতরে—কখনো পূর্ব কখনো পশ্চিম বাঙলায়, কিন্তু সর্বত্রই চলে ঐ এক নিয়ম এক রীতি। সেখানে হয় সবই, হয় না কেবল পরিচয়। হয় না শুধু ভাবের আদান-প্রদান, বাকী থেকে যায় পরস্পরের মন জানাজানি। তার অবকাশ কৈ? বড় বড় সুনিশ্চিত সারবান প্রবন্ধের ভারে ভারাক্রান্ত সম্মিলনী মেলামেশার সময় করবে কি, নিশ্বাস নেবার ফুরসত করে উঠতে পারে না। সেখানে না থাকে পান-তামাক, না থাকে চা। নড়চড়ার জো নেই পাছে শৃঙ্খলা নষ্ট হয়, হাস্য-পরিহাসের সাহস নেই পাছে বে-আদপি প্রকাশ পায়, আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ মেলে না পাছে গুরু-গম্ভীর প্রবন্ধের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। যেন আদালতের আসামীর মতো সেখানে সবাই গম্ভীর সবাই বিপন্ন। আড়চোখে সবাই চেয়ে দেখে প্রবন্ধের খাতায় আরও ক’পাতা লেখা পড়তে তখনও বাকি। তার পরে আসে সভাভঙ্গের পালা—চলে ইস্টিশানে ছুটোছুটি। শুধু পালাবার পথ নেই যাদের তারাই কেবল ক্লান্ত দেহ-মনে ফিরে চলে বাসায়।
এই হচ্ছে মোটামুটি সাহিত্য-সম্মিলনীর বিবরণ। তাই প্রার্থনা জানিয়েছিলাম. এই ফর্দে আরও একটি বিড়ম্বনার কাহিনী যেন ফরিদপুরের অদৃষ্টেও সংযুক্ত হয়ে না যায়।
বিগত দিনের সাহিত্যিক অনুষ্ঠানগুলিকে স্মরণ করে এ প্রশ্ন আজ আমি করবো না সেই সকল লেখাগুলির কোন্ সদ্গতি অদ্যাবধি হয়েছে,—কারণ, এ জিজ্ঞাসা বাহুল্য।
আপনাদের হয়ত মনে হবে কিছু একটা সারালো ও ধারালো লেখা আমার লিখে আনা উচিত ছিল যা ছাপালে হয় সভাপতির অভিভাষণ, কিন্তু তা আমি করি নি। পারিনে বলে নয়, সময় ছিল না বলে নয়, অহেতুক ও অকারণ বলেই লিখিনি। তবে এটা কি? এ শুধু মুখে-মুখে বলার শক্তি নেই বলেই এই সভায় উপস্থিত হবার অনতিকাল পূর্বে দু-ছত্র টুকে এনেছি।
প্রশ্ন উঠতে পারে এ সভার লক্ষ্য কি? উদ্দেশ্য কি? আমার মনে হয় লক্ষ্য শুধু এই কথাটা মনে রাখা এ আমাদের উৎসব, এ আমাদের আনন্দের অনুষ্ঠান। জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে আসিনি, যুক্তি – তর্কের বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্য অবলম্বন করে এখানে এসে আমরা সমবেত হইনি। সাহিত্য-চর্চার ক্ষেত্র আর যেখানেই কেন না হোক এখানে নয়। এই কথাটাই আজ আমার অন্তর বলে। তাই আমি এসেছি উৎসবের মন নিয়ে, আমি এসেছি হৃদয়ের আদান-প্রদানে পরস্পরের সুনিবিড় পরিচয় নিতে। এ উপলক্ষ না ঘটলে হয়ত কোনদিন আমাদের আপনাদের দেশে আসা হত না, আপনাদের সৌজন্য সহৃদয়তা সৌভ্রাত্র ও আতিথ্যের স্বাদ গ্রহণ করা ভাগ্যে জুটতো না। এই আমাদের পরম লাভ, এই আমাদের আজকের সভার সার্থকতা। আরও একটা কথা বড় করে আজ আমার বারংবার মনে হয়। মাতৃভাষার সেবক আমরা,—সাহিত্যের পুণ্য মিলনক্ষেত্র ছাড়া এতগুলি হিন্দু-মুসলমান ভাই-বোনেরা আমরা একাসনে বসে এমনভাবে মিলতে পারতাম আর কোন্ সভাতলে?
আর একটা কথা বলার বাকি আছে। সে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করা। আমার গভীর আনন্দ ও তৃপ্তির কথা শতমুখে বলা। কিন্তু মুখ আমার একটি, তার সাধ্য সীমাবদ্ধ। এই ক্ষোভের কথাটাও জানিয়ে রেখে আমি বিদায় গ্রহণ করলাম।
সাহিত্যের আর একটা দিক
কল্যাণীয়া জাহান-আরা।
তোমার বার্ষিক পত্রিকায় সামান্য কিছু একটা লিখে দিতে অনুরোধ করেছ। আমার বর্তমান অসুস্থতার মধ্যে হয়ত সামান্যই একটু লেখা চলে। ভাবছিলাম, সাহিত্যের ধর্ম, রূপ, গঠন, সীমানা, এর তত্ত্ব প্রভৃতি নিয়ে মাঝে মাঝে অল্প-বিস্তর আলোচনা হয়ে গেছে, কিন্তু এর আর একটা দিকের কথা প্রকাশ্যে আজও কেউ বলেন নি। সে এর প্রয়োজনের দিক,—এর কল্যাণ করার শক্তির সম্বন্ধে। এ কথা বোধ করি বহু লোকেই স্বীকার করবেন যে, সাহিত্য-রসের মধ্যে দিয়ে পাঠকের চিত্তে যেমন সুবিমল আনন্দের সৃষ্টি করে, তেমনি পারে করতে মানুষের বহু অন্তর্নিহিত কুসংস্কারের মূলে আঘাত। এরই ফলে মানুষ হয় বড়, তার দৃষ্টি হয় উদার, তার সহিষ্ণু ক্ষমাশীল মন সাহিত্য-রসের নূতন সম্পদে ঐশ্বর্যবান হয়ে ওঠে।
বাঙলাদেশের একটা বড় সমাজের মধ্যে এর ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে। সাহিত্য-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে এখানে ক্ষোভ ও বেদনা উত্তরোত্তর যেন বেড়ে উঠেচে বলেই মনে হয়। আমি তোমাদের মুসলমান-সমাজের কথাই বলছি। রাগের উপর কেউ কেউ ভাষাটাকে বিকৃত করে তুলতেও যেন পরাঙ্মুখ নন, এমনি চোখে ঠেকে। অজুহাত তাঁদের নেই তা নয়, কিন্তু রাগ পড়লে একদিন নিজেরাই দেখতে পাবেন, অজুহাতের বেশী ও সে নয়। যে-কারণেই হোক, এতদিন বাঙলাদেশের হিন্দুরাই শুধু সাহিত্য-চর্চা করে এসেছেন। মুসলমান-সমাজ দীর্ঘকাল এদিকে উদাসীন ছিলেন। কিন্তু সাধনার ফল ত একটা আছেই, তাই বাণী-দেবতা বর দিয়ে এসেছেনও এঁদেরকে। মুষ্টিমেয় সাহিত্য-রসিক মুসলমান সাধকের কথা আমি ভুলিনি, কিন্তু কোনদিনই সে বিস্তৃত হতে পারেনি। তাই, ক্রোধের বশে তোমাদের কেউ কেউ নাম দিয়েছেন এর হিন্দু-সাহিত্য। কিন্তু আক্ষেপের প্রকাশ ত যুক্তি নয়।
যদিচ, বলা চলে, সাহিত্যিকদের মধ্যে কয়জন তাঁদের রচনায় মুসলমান-চরিত্র এঁকেছেন, ক’টা জায়গায় এতবড় বিরাট সমাজের সুখ-দুঃখের বিবরণ বিবৃত করেছেন। কেমন করে তাঁদের সহানুভূতি পাবেন, কিসে তাঁদের হৃদয় স্পর্শ করবে! স্পর্শ করেনি তা জানি, বরঞ্চ উলটোটাই দেখা যায়। ফলে ক্ষতি যা হয়েছে তা কম নয়, এবং আজ এর একটা প্রতিকারের পথও খুঁজে দেখতে হবে।
কিছুকাল পূর্বে আমার একটি নবীন মুসলমান বন্ধু এই আক্ষেপ আমার কাছে করেছিলেন। নিজে তিনি সাহিত্যসেবী, পণ্ডিত অধ্যাপক, সাম্প্রদায়িক মালিন্য তাঁর হৃদয়কে মলিন, দৃষ্টিকে আজও আবিল করেনি। বললেন, হিন্দু ও মুসলমান এই দুই বৃহৎ জাতি, একই দেশে, একই আবহাওয়ার মধ্যে পাশাপাশি প্রতিবেশীর মত বাস করে, একই ভাষা জন্মকাল থেকে বলে, তবুও এমনি বিচ্ছিন্ন, এমনি পর হয়ে আছে যে, ভাবলেও বিস্ময় লাগে। সংসার ও জীবনধারণের প্রয়োজনে বাইরের দেনা-পাওনা একটা আছে, কিন্তু অন্তরের দেনা-পাওনা একেবারে নেই বললেও মিথ্যে বলা হয় না। কেন এমন হয়েছে, এ গবেষণার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আজ এই বিচ্ছেদের অবসান, এই দুঃখময় ব্যবধান ঘুচোতেই হবে। না হলে কারও মঙ্গল নেই।
বললাম, এ কথা মানি, কিন্তু এই দুঃসাধ্য-সাধনের উপায় কি স্থির করেছ?
তিনি বললেন, উপায় হচ্ছে একমাত্র সাহিত্য। আপনারা আমাদের টেনে নিন। স্নেহের সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের কথা বলুন। নিছক হিন্দুর জন্যেই হিন্দু-সাহিত্য রচনা করবেন না। মুসলমান পাঠকের কথাও একটুখানি মনে রাখবেন। দেখবেন, বাইরের বিভেদ যত বড়ই দেখাক, তবু একই আনন্দ একই বেদনা উভয়ের শিরার রক্তেই বয়।
বললাম, এ কথা আমি জানি। কিন্তু অনুরাগের সঙ্গে বিরাগ, প্রশংসার সঙ্গে তিরস্কার, ভালো-কথার সঙ্গে মন্দ-কথাও যে গল্প-সাহিত্যের অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু এ ত তোমরা না করবে বিচার, না করবে ক্ষমা। হয়ত এমন দণ্ডের ব্যবস্থা করবে, যা ভাবলেও শরীর শিউরে ওঠে। তার চেয়ে যা আছে, সেই ত নিরাপদ।
তার পরে দু-জনেই ক্ষণকাল চুপ করে রইলাম। শেষে বললাম, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত বলবেন, আমরা ভীতু, তোমরা বীর, তোমরা হিন্দুর কলম থেকে নিন্দা বরদাস্ত করো না এবং প্রতিশোধ যা নাও তাও চূড়ান্ত। এও মানি, এবং তোমাদের বীর বলতেও ব্যক্তিগতভাবে আমার আপত্তি নেই। তোমাদের সম্বন্ধে আমাদের ভয় ও সঙ্কোচ সত্যিই যথেষ্ট। কিন্তু এ-ও বলি, এই বীরত্বের ধারণা তোমাদের যদি কখনও বদলায়, তখন দেখবে তোমরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছ সবচেয়ে বেশী।
তরুণ বন্ধুর মুখ বিষণ্ণ হয়ে এলো, বললেন, এমনি non-co-operationই কি তবে চিরদিন চলবে?
বললাম, না, চিরদিন চলবে না; কারণ, সাহিত্যের সেবক যাঁরা তাঁদের জাতি, সম্প্রদায় আলাদা নয়, মূলে,—অন্তরে তাঁরা এক। সেই সত্যকে উপলব্ধি করে এই অবাঞ্ছিত সাময়িক ব্যবধান আজ তোমাদেরই ঘুচোতে হবে।
বন্ধু বললেন, এখন থেকে সেই চেষ্টাই করব।
বললাম, করো। তোমার চেষ্টার ’পরে জগদীশ্বরের আশীর্বাদ প্রতিদিন অনুভব করবে।
ইতি, ১২ ই মাঘ ১৩৪২। ( ‘বর্ষবাণী ’ ৩য় বর্ষ, ১৩৪২)
সাহিত্যের মাত্রা
‘সাহিত্যের মাত্রা’
কল্যাণীয়েষু,—শ্রাবণের [১৩৪০] ‘পরিচয়’ পত্রিকায় শ্রীমান্ দিলীপকুমারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র—সাহিত্যের মাত্রা—সম্বন্ধে তুমি [‘পরিচারক’-সম্পাদক শ্রীঅতুলানন্দ রায়] আমার অভিমত জানতে চেয়েছ। এ চিঠি ব্যক্তিগত হলেও যখন সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়েছে, তখন এরূপ অনুরোধ হয়ত করা যায়, কিন্তু অনেক চার-পাতা-জোড়া চিঠির শেষছত্রের ‘কিছু টাকা পাঠাইবার’ মত এরও শেষ ক’লাইনের আসল বক্তব্য যদি এই হয় যে, ইয়োরোপ তার যন্ত্রপাতি, ধন-দৌলত, কামান-বন্দুক, মান-ইজ্জত সমেত অচিরে ডুববে, তবে অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে এই কথাই মনে করবো যে, বয়েস ত অনেক হ’ল, ও-বস্তু কি আর চোখে দেখে যাবার সময় পাব!
কিন্তু এদের ছাড়াও কবি আরও যাদের সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, তোমাদের সন্দেহ তার মধ্যে আমিও আছি। অসম্ভব নয়। এ প্রবন্ধে কবির অভিযোগের বিষয় হ’ল ওরা ‘মত্ত হস্তী’, ‘ওরা বুলি আওড়ালে’, ‘পালোয়ানি করলে’, ‘কসরৎ কেরামত দেখালে’, ‘প্রব্লেম সল্ভ করলে’, ‘অতএব ওদের’ ইত্যাদি ইত্যাদি।
এই কথাগুলো যাদেরকেই বলা হোক, সুন্দরও নয়, শ্রুতিসুখকরও নয়। শ্লেষবিদ্রূপের আমেজে মনের মধ্যে একটা ইরিটেশান আনে। তাতে বক্তারও উদ্দেশ্য যায় ব্যর্থ হয়ে, শ্রোতারও মন যায় বিগড়ে। অথচ ক্ষোভপ্রকাশ যেমন বাহুল্য, প্রতিবাদও তেমন বিফল। কার তৈরি-করা বুলি পাখির মত আওড়ালুম, কোথায় পালোয়ানি করলুম, কি ‘খেল্’ দেখালুম, ক্রুদ্ধ কবির কাছে এ-সকল জিজ্ঞাসা অবান্তর। আমার ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। খেলার মাঠে কেউ রব তুলে দিলেই হল অমুক গু মাড়িয়েছে। আর রক্ষে নেই,—কোথায় মাড়ালুম, কে বললে, কে দেখেচে, ওটা গু নয়, গোবর—সমস্ত বৃথা। বাড়ি এসে মায়েরা না নাইয়ে, মাথায় গঙ্গাজলের ছিটে না দিয়ে আর ঘরে ঢুকতে দিতেন না। কারণ, ও যে গু মাড়িয়েচে! এও আমার সেই দশা।
‘সাহিত্যের মাত্রা’ই বা কি, আর অন্য প্রবন্ধই বা কি, এ কথা অস্বীকার করিনে যে, কবির এই ধরনের অধিকাংশ লেখাই বোঝবার মত বুদ্ধি আমার নেই। তাঁর উপমা উদাহরণে আসে কল – কবজা, আসে হাট-বাজার, হাতি-ঘোড়া, জন্তু-জানোয়ার—ভেবেই পাইনে মানুষের সামাজিক সমস্যায় নরনারীর পরস্পরের সম্বন্ধবিচারে ওরা সব আসেই বা কেন এবং এসেই বা কি প্রমাণ করে? শুনতে বেশ লাগসই হলেই ত তা যুক্তি হয়ে ওঠে না।
একটা দৃষ্টান্ত দিই। কিছুদিন পূর্বে হরিজনদের প্রতি অবিচারে ব্যথিত হয়ে তিনি প্রবর্তক-সঙ্ঘের মতিবাবুকে একখানা চিঠি লিখেছিলেন। তাতে অনুযোগ করেছিলেন যে, ব্রাহ্মণীর পোষা বিড়ালটা এঁটো-মুখে গিয়ে তাঁর কোলে বসে, তাতে শুচিতা নষ্ট হয় না—তিনি আপত্তি করেন না। খুব সম্ভব করেন না, কিন্তু তাতে হরিজনদের সুবিধা হল কি? প্রমাণ করলে কি? বিড়ালের যুক্তিতে এ কথা ত ব্রাহ্মণীকে বলা চলা না যে, যে-হেতু অতিনিকৃষ্ট-জীব বেড়ালটা গিয়ে তোমার কোলে বসেছে, তুমি আপত্তি করোনি, অতএব অতি-উৎকৃষ্ট-জীব আমিও গিয়ে তোমার কোলে বসব, তুমি আপত্তি করতে পারবে না। বেড়াল কেন কোলে বসে, পিঁপড়ে কেন পাতে ওঠে, এ-সব তর্ক তুলে মানুষের সঙ্গে মানুষের ন্যায়-অন্যায়ের বিচার হয় না। এ-সব উপমা শুনতে ভাল, দেখতেও চকচক করে, কিন্তু যাচাই করলে দাম যা ধরা পড়ে, তা অকিঞ্চিৎকর। বিরাট ফ্যাক্টরীর প্রভূত বস্তুপিণ্ড উৎপাদনের অপকারিতা দেখিয়ে মোটা নভেলও অত্যন্ত ক্ষতিকর, এ কথা প্রতিপন্ন হয় না।
আধুনিককালের কল-কারখানাকে নানা কারণে অনেকেই আজকাল নিন্দে করেন, রবীন্দ্রনাথও করেছেন—তাতে দোষ নেই। বরঞ্চ ওইটেই হয়েছে ফ্যাশন। এই বহু-নিন্দিত বস্তুটার সংস্পর্শে যে মানুষগুলো ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় এসে পড়েছে, তাদের সুখ-দুঃখের কারণগুলোও হয়ে দাঁড়িয়েছে জটিল—জীবন-যাত্রার প্রণালীও গেছে বদলে, গাঁয়ের চাষাদের সঙ্গে তাদের হুবহু মেলে না। এ নিয়ে আপসোস করা যেতে পারে, কিন্তু তবু যদি কেউ এদেরই নানা বিচিত্র ঘটনা নিয়ে গল্প লেখে, তা সাহিত্য হবে না কেন?
কবিও বলেন না যে হবে না। তাঁর আপত্তি শুধু সাহিত্যের মাত্রা লঙ্ঘনে। কিন্তু এই মাত্রা স্থির হবে কি দিয়ে? কলহ দিয়ে, না কটুকথা দিয়ে? কবি বলেছেন—স্থির হবে সাহিত্যের চিরন্তন মূল নীতি দিয়ে। কিন্তু এই ‘মূল নীতি’ লেখকের বুদ্ধির অভিজ্ঞতা ও স্বকীয় রসোপলব্ধির আদর্শ ছাড়া আর কোথাও আছে কি? চিরন্তনের দোহাই পাড়া যায় শুধু গায়ের জোরে আর কিছুতে নয়। ওটা মরীচিকা।
কবি বলছেন, “ উপন্যাস-সাহিত্যেরও সেই দশা। মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েছে।” কিন্তু প্রত্যুত্তরে কেউ যদি বলে, “উপন্যাস-সাহিত্যের সে দশা নয়, মানুষের প্রাণের রূপ চিন্তার স্তূপে চাপা পড়েনি, চিন্তার সূর্যালোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে,” তাকে নিরস্ত করা যাবে কোন্ নজির দিয়ে? এবং এরই সঙ্গে আর একটা বুলি আজকাল প্রায়ই শোনা যায়, তাতে রবীন্দ্রনাথও যোগান দিয়েছেন এই বলে যে, “যদি মানুষ গল্পের আসরে আসে, তবে সে গল্পই শুনতে চাইবে, যদি প্রকৃতিস্থ থাকে।” বচনটি স্বীকার করে নিয়েও পাঠকেরা যদি বলে—হাঁ, আমরা প্রকৃতিস্থই আছি, কিন্তু দিন-কাল বদলেছে এবং বয়েসও বেড়েছে; সুতরাং রাজপুত্র ও ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্পে আমাদের মন ভরবে না, তা হলে জবাবটা যে তাদের দুর্বিনীত হবে, এ আমি মনে করিনে। তারা অনায়াসে বলতে পারে, গল্পে চিন্তাশক্তির ছাপ থাকলেই তা পরিত্যাজ্য হয় না কিংবা বিশুদ্ধ গল্প লেখার জন্যে লেখকের চিন্তাশক্তি বিসর্জন দেবারও প্রয়োজন নাই।
কবি মহাভারত ও রামায়ণের উল্লেখ করে ভীষ্ম ও রামের চরিত্র আলোচনা করে দেখিয়েছেন, ‘বুলি’র খাতিরে ও-দুটো চরিত্রই মাটি হয়ে গেছে। এ নিয়ে আমি আলোচনা করব না, কারণ ও-দুটো গ্রন্থ শুধু কাব্যগ্রন্থই নয় ধর্মপুস্তক ত বটেই, হয়ত বা ইতিহাসও বটে। ও-দুটি চরিত্র কেবলমাত্র সাধারণ উপন্যাসের বানানো চরিত্র নাও হতে পারে, সুতরাং সাধারণ কাব্য-উপন্যাসের গজকাঠি নিয়ে মাপতে যেতে আমার বাধে।
চিঠিটায় ইন্টালেক্ট শব্দটার বহু প্রয়োগ আছে। মনে হয় যেন কবি বিদ্যে ও বুদ্ধি উভয় অর্থেই শব্দটার ব্যবহার করেছেন। প্রব্লেম শব্দটাও তেমনি। উপন্যাসে অনেক রকমের প্রব্লেম থাকে, ব্যক্তিগত, নীতিগত, সামাজিক, সাংসারিক, আর থাকে গল্পের নিজস্ব প্রব্লেম, সেটা প্লটের। এর গ্রন্থিই সবচেয়ে দুর্ভেদ্য। কুমার সম্ভবের প্রব্লেম, উত্তরকাণ্ডে রামভদ্রের প্রব্লেম, ডল্স হাউসের নোরার প্রব্লেম, অথবা যোগাযোগের কুমুর প্রব্লেম একজাতীয় নয়। যোগাযোগ বইখানা যখন ‘বিচিত্রা’য় চলছিল এবং অধ্যায়ের পর অধ্যায় কুমু যে হাঙ্গামা বাধিয়েছিল, আমি ত ভেবেই পেতুম না ঐ দুর্ধর্ষ প্রবলপরাক্রান্ত মধুসূদনের সঙ্গে তার টাগ-অফ-ওয়ারের শেষ হবে কি করে? কিন্তু কে জানত সমস্যা এত সহজ ছিল—লেডি ডাক্তার মীমাংসা করে দেবেন একমুহূর্তে এসে। আমাদের জলধর দাদাও প্রব্লেম দেখতে পারেন না, অত্যন্ত চটা। তাঁর একটা বইয়ে এমনি একটা লোক ভারী সমস্যার সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু তার মীমাংসা হয়ে গেল অন্য উপায়ে। ফোঁস করে একটা গোখরো সাপ বেরিয়ে তাকে কামড়ে দিলে। দাদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, এটা কি হল? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, কেন, সাপে কি কাউকে কামড়ায় না?
পরিশেষে আর একটা কথা বলবার আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, “ইব্সেনের নাটকগুলি ত একদিন কম আদর পায়নি, কিন্তু এখনি কি তার রং ফিকে হয়ে আসেনি, কিছুকাল পরে সে কি আর চোখে পড়বে?” না পড়তে পারে, কিন্তু তবুও এটা অনুমান, প্রমাণ নয়। পরে একদিন এমনও হতে পারে, ইব্সেনের পুরানো আদর আবার ফিরে আসবে। বর্তমান কালই সাহিত্যের চরম হাইকোর্ট নয়।