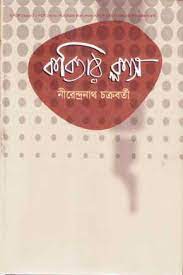- বইয়ের নামঃ কবিতার ক্লাস
- লেখকের নামঃ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
- প্রকাশনাঃ নবযুগ প্রকাশনী
- বিভাগসমূহঃ কাব্যগ্রন্থ
০১. কেউ কেউ কবি নয়, সকলেই কবি
এই বইয়ের নাম দিয়েছি ‘কবিতা ক্লাস’। এতে চমকাবার কিছু নেই। অনেকে মনে করেন যে, কবিতা একটি অপার্থিব দিব্য বস্তু, এবং তাকে আয়ত্ব করবার জন্যে, মুনিঋষিদের মতো, নির্জন পাহাড়ে-পর্বতে কিংবা বনে-জঙ্গলে গিয়ে তপস্যা করতে হয়। আমি তা মনে করি না। আমার বিশ্বাস, জাতে যদিও আলাদা, তবু কবিতা-ও সাংসারিক বিষয় ছাড়া আর-কিছুই নয়, আমাদের এই সাংসারিক জীবনের মধ্যেই তার বিস্তর উপাদান ছড়িয়ে পড়ে আছে, এবং ইস্কুল খুলে, ক্লাস নিয়ে, রুটিনমাফিক আমরা যেভাবে ইতিহাস কি ধারাপাত কি অঙ্ক শেখাই, ঠিক তেমনি করেই কবিতা লেখার কায়দাগুলো শিখিয়া দেওয়া যায়। ‘কায়দা’ না-বলে অনেকে বলবেন ‘কলাকৌশল’, তা বলুন, কথাটা তার ফলে আর-একটু সম্ভ্রান্ত শোনাবে ঠিকই, কিন্তু মূল বক্তব্যের কোন ইতরবিশেষ হবে না। বিশ্বাস করুন চাই না-করুন, কবিতা লেখা সত্যিই খুব কঠিন কাণ্ড নয়।
সেই তুলনায় পদ্য লেখা আরও সহজ। শুধু কায়দাগুলো রপ্ত করা চাই, ঘাঁতঘোঁত জেনে নেওয়া চাই। কবিতা আর পদ্যের তফাত কোথায়, এক্ষুনি সেই তর্কে ঢুকে ব্যাপারটালে ঘোরালো করে তুলতে চাই না। তার চাইতে বরং জিজ্ঞেস করি, আপনার বয়স যখন অল্প ছিল, তখন ছোটপিসি কি ন-মাসি কি সেজদির বিয়ের সময়ে কি আপনার একখানা উপহার লিখবার ইচ্ছে হয়নি? হয়তো হয়েছিল। হয়তো ভেবেছিলেন, “বাঃ কী মজা, বাঃ কী মজা, খাব লুচি মন্ডা গজা” ইত্যাদি সব উপাদেয় খাবারদাবারের কথা দিয়ে লাইন-কয় লিখে তারপর “বিভুপদে এ-মিনতি—“ জানবেন যে, নবদম্পতি যেন চিরকাল সুখে থাকে।
কিন্তু হায়, শেষ পর্যন্ত আর হয়তো লেখা হয়নি। হবে কী করে? ‘মজা’র সঙ্গে ‘গজা’র মিলটাই তখন মনে পড়েনি যে। আর তাই, কড়িকাঠের দিকে ঘণ্টাখানেক তাকিয়ে থেকে, এবং নতুন-কেনা মেড-ইন-ব্যাভেরিয়া পেনসিলের গোড়াটাকে চিবিয়ে ছাতু করে, শেষপর্যন্ত হয়তো ‘ধুত্তোর’ বলে আপনি উঠে পড়েছিলেন। মনে-মনে খুব সম্ভব বলেছিলেন, “ওসব উপহার-টুপহার লেখার চাইতে বরং মুদির দোকানের খাতা লেখা অনেক সহজ।”
মুদির দোকানের প্রসঙ্গে একটা পুরোনো কথা মনে পড়ল। বছর পঞ্চাশেক আগেকার ঘটনা। আমার বয়স তখন বছর-দশেক। সেইসময়ে আঁক কষতে-কষতে শেলেটের উপরে আমি একটা পদ্য লিখেছিলুম। তার আরম্ভটা এইরকম—
আজ বড়ো আনন্দ হইয়াছে।
দেখিয়াছি, রান্নাঘরে কই আছে।
অর্থাৎ আমি বলতে চেয়েছিলুম যে, মা যখন কইমাছ রান্না করছেন, তখন দুপুরের ভোজনপর্বটা বেশ জমাট হবে, সুতরাং আজ আমার বড়োই আনন্দের দিন। আনন্দ অবশ্য দীর্ঘস্থায়ী হল না; এক জ্যাঠতুতো দাদা এসে চুলের মুঠি ধরে আমাকে শূন্যে তুলে ফেললেন, তারপর বাঁ হাতে আমাকে শূন্যে ঝুলিয়ে রেখে ডান হাতে একটা চড় কষালেন, তারপর বললেন, “হতচ্ছাড়া, তোমাকে আঁক কষতে দেওয়া হয়েছে, আর তুমি কিনা বসে-বসে কাব্যি করছ? এই আমি বলে রাখলুম, পরে তোমাকে মুদির দোকানের খাতা লিখে পেট চালাতে হবে।”
বাজে কথা। যে-ছেলে আঁক কষতে ভয় পায়, তার পক্ষে মুদির দোকানের খাতা লেখা সম্ভব নয়। চাল-ডাল-গোলমরিচ-জিরে-হলুদ-পাঁচফোড়নের হিসেব রাখা কি চাট্টিখানি ব্যাপার? সে-কাজ সকলে পারে না। তার জন্যে সাফ মাথা চাই। সেই তুলনায় বরং কবিতা লেখা অনেক সহজ। কবিতা লেখবার জন্যে, আর যা-কিছুরই দরকার থাক, মাথাটাকে সাফ রাখবার কোনও দরকার নেই। বরং, সত্যি বলতে কী, মাথার মধ্যে একটু গোলমাল থাকলেই ভালো। কিন্তু না, মাথার প্রসঙ্গ এইখানেই ছেদ টানা যাক, কেন-না বিশুদ্ধ আগমার্কা কবিরা হয়তো এইটুকু শুনেই চোখ রাঙাতে শুরু করেছেন, বাকিটুকু শুনলে তাঁরা আমাকে আস্ত রাখবেন না। তার চাইতে বরং যে-কথা বলছিলুম, তা-ই বলি।
আমার বলবার কথাটা এই যে, অল্প একটু চেষ্টা করলে যে-কেউ কবিতা লিখতে পারে। আমার মাসতুতো ভাইয়ের ছোটছেলেটির কথাই ধরুন। গুণধর ছেলে। টুললিফাই করেছে, পরীক্ষার হলে বোমা ফাটিয়েছে, গার্ডকে ‘জান খেয়ে নেব’ বলে শাসিয়েছে, উপরন্তু চাঁদা তুলে, মাইক বাজিয়ে সরস্বতী পুজো করে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে তুষ্ট করেছে, তবু—এতরকম কাণ্ড করেও—স্কুল-ফাইনালের পাঁচিলটা সে টপকাতে পারেনি, তিন বার পরীক্ষা দিয়েছিল। তিন বারই ফেল। এখন সে আমাদের হাটবাজার করে দেয়, হরিণঘাটার ডিপো থেকে দুধ আনে, পঞ্চাশ রকমের ফাইফরমাশ খাটে, এখানে-ওখানে ভুল-ইংরেজিতে চাকরির দরখাস্ত পাঠায়, এবং—
এবং কবিতা লেখে। তা সে-ও যদি কবি হতে পারে, তবে আপনি পারবেন না কেন?
আমার গিন্নির খুড়তুতো ভাই এক সওদাগরি আপিসের বড়োবাবু। আগে সে-ও কবিতা লিখত, কিন্তু আপিসে তাই নিয়ে হাসাহাসি হওয়ায় এবং বড়োসাহেব তাকে একদিন চোখ পাকিয়া “হোয়াট্’স দিস্ আয়া’ম্ হিয়ারিং অ্যাবাউট ইউ” বলায়, কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে সে এখন গোয়েন্দা-গল্পের ভক্ত হয়েছে। তার কাছে সেদিন একটা ইংরেজি বই দেখলুম। বইয়ের নামে বুচার্ বেকার্ মার্ডার মেকার্। অর্থ অতি পরিষ্কার। যে-কেউ খুন করতে পারে। নৃশংস কসাইও পারে, আবার নিরীহ রুটিওয়ালাও পারে। খুন করবার জন্যে যে একটা আলাদা রকমের লোক হওয়া চাই, তা নয়।
তুলনাটা হয়তো একটু অস্বস্তিকর হয়ে যাচ্ছে, তবু বলি কবিতার ব্যাপারেও তা-ই। কবিতা লিখবার জন্যে আলাদা রকমের মানুষ হবার দরকার নেই। রামা শ্যামা যদু মধু প্রত্যেকেই (ইচ্ছে করলে এবং কায়দাগুলোকে একটু খেটেখুটে রপ্ত করে নিলে) ছন্দ ঠিক রেখে, লাইনের পর লাইন মিলিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতে পারে।
তা জন্যে, বলাই বাহুল্য, কিছু জিনিস চাই, এবং কিছু জিনিস চাই না।
আগে বলি কী কী চাই না—
১) কবি হবার জন্যে লম্বা-লম্বা চুল রাখবার দরকার নেই। ওটা হিপি হবার শর্ত হতে পারে, কিন্তু কবি হবার শর্ত নয়। পরীক্ষা করে দেখে গেছে, চুল খুব ছোটো করে ছেঁটেও কিংবা মাথা একেবারে ন্যাড়া করে ফেলেও কবিতা লেখা যায়। চুলের সঙ্গে বিদ্যুতের সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে, কবিতার নেই।
২) সর্বক্ষণ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকবার দরকার নেই। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মাটির দিকে তাকিয়েও কবিতা লেখা যায়। সবচাইতে ভালো হয়, যদি অন্য কোনও দিকে না তাকিয়ে শুধু খাতার দিকে চোখ রাখেন।
৩) কখন চাঁদ উঠবে, কিংবা মলয় সমীর বইবে, তার প্রতীক্ষায় থাকবার দরকার নেই। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, অমাবস্যার রাত্রেও কবিতা লেখা যায়, এবং মলয় সমীরের বদলে ফ্যানের হাওয়ায় কবিতা লিখলে তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না।
৪) ঢোলা-হাতা পাঞ্জাবি পরবার দরকার নেই। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, স্যানডো গেঞ্জি গায়ে দিয়েও, কিংবা একেবারে আদুর গায়েও, কবিতা লেখা সম্ভব।
এইবার বলি, কবিতা লিখতে হলে কী কী চাই।
বিশেষ-কিছু চাই না। দরকার শুধু—
১) কিছু কাগজ (লাইন-টানা হলেও চলে, না-হলেও চলে)।
২) একটি কলম (যে-কোনও শস্তা কলম হলেও চলবে) অথবা একটি পেনসিল এবং–
৩) কিছু সময়।
কিন্তু এতসব কথা আমি বলছি কেন? কবিতার কৌশলগুলিকে সর্বজনের হাতের মুঠোয় এনে না-দিয়ে কি আমার তৃপ্তি নেই? সত্যিই নেই। ইংরেজিতে ‘পোয়্ট্রি ফর দি কমন ম্যান’ বলে একটা কথা আছে। আমার ইচ্ছে, কমন ম্যানদেরও আমি পোয়্ট বানিয়ে ছাড়ব। পরশুরামের কথা মনে পড়ছে। তাঁর প্রতিজ্ঞা ছিল, পৃথিবীকে একেবারে নিঃক্ষত্রিয় করে ছাড়বেন। কিন্ত, না-পারবার হেতুটা যা-ই হোক, কাজটা তিনি পারতে-পারতেও পারেননি। বিশ্বসংসারকে যাঁরা নিষ্কবি করে ছাড়তে চান (অনেকেই চান), তাঁরাও সম্ভবত শেষ পর্যন্ত পেরে উঠবেন না।
আমার প্রতিজ্ঞাটা অন্য রকমের। আমি ঠিক করেছি, বাংলা দেশে সব্বাইকে আমি কবি বানাব। দেখি পারি কি না।
কবিতা লিখবার জন্যে কী কী চাই, তা তো একটু আগেই বলেছি। চাই কাগজ, চাই কলম (কিংবা পেনসিল), চাই সময়। তা আশা করি কাগজ-কলম আপনারা জোগাড় করতে পেরেছেন। বাকি রইল সময়। তা-ও নিশ্চয়ই আপনাদের আছে। রেশনের দোকানে লাইন না-লাগিয়ে, এই যে আপনারা গুটিগুটি ‘কবিতার ক্লাস’-এ এসে হাজির হয়েছেন, এতেই বুঝতে পারছি যে, সময়ের বিশেষ অভাব আপনাদের নেই।
সুতরাং ‘দুর্গা দুর্গা’ বলে শুরু করা যাক। অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।
আগেই বলি, কবিতার মধ্যে তিনটি জিনিস থাকা চাই। কাব্যগুণ, ছন্দ, মিল।
বিনা ডিমে যেমন ওমলেট হয় না, তেমনই কাব্যগুণ না থাকলে কবিতা হয় না। তার প্রমাণ হিসেবে আসুন, আমার সেই মাসতুতো ভাইয়ের ছোটোছেলের লেখা চারটে লাইন শোনাই:
সূর্য ব্যাটা বুর্জোয়া যে,
দুর্যোধনের ভাই।
গর্জনে তার তুর্য বাজে,
তর্জনে ভয় পাই।
বলা বাহুল্য, এটা কবিতা হয়নি। তার কারণ, ছন্দ আর মিলের দিকটা ঠিকঠাক আছে বটে, কিন্তু কাব্যগুণ এখানে আদপেই নেই। এবং কাব্যগুণ না-থাকায় দেখা যাচ্ছে ব্যাপারটা নেহাতই বাক্যের ব্যায়াম হয়ে উঠেছে।
এবারে মিলের কথায় আসা যাক। মিল না-রেখে যে কবিতা লেখা যায় না, তা অবশ্য নয়, তবু যে আমি মিলের উপর এত জোর দিচ্ছি তার কারণ:
১) প্রথমেই যদি আপনি মিল-ছাড়া কবিতা লিখতে শুরু করেন, তাহলে অনেকেই সন্দেহ করবে যে, মিল-এ সুবিধে হয়নি বলেই আপনি অ-মিলের লাইনে এসেছেন। সেটা খুব অপমানের ব্যাপার।
২) মিল জিনিসটাকে প্রথম অবস্থায় বেশ ভালো করে দখল করা চাই। তবেই সেটাকে ছেড়ে দিয়েও পরে ভালো কবিতা লেখা সম্ভব হবে। যেমন বড়ো-বড়ো লিখিয়েদের মধ্যে অনেকেই অনেকসময়ে ব্যাকরণের গণ্ডির বাইরে পা বাড়িয়ে চমৎকার লেখেন, এ-ও ঠিক তেমনই। ব্যাকরণ বস্তুটাকে প্রথমে বেশ ভালো করে মান্য করা চাই, তবেই পরে সেটাকে দরকারমতো অমান্য করা যায়। ঠিক তেমনি, পরে যাতে মিলের বেড়া ভাঙা সহজ হয়, তারই জন্যে প্রথম দিকে মিলটাকে বেশ আচ্ছা করে রপ্ত করতে হবে।
ছন্দ কিন্তু সবসময়ই চাই। আগেও চাই, পরেও চাই। আসলে আমার ক্লাসে আমি ছন্দের কথাই বলব। সেই বিচারে ‘কবিতার ক্লাস’ না-বলে একে ‘ছন্দের ক্লাস’ও বলা যেতে পারত। তাতে কিছু ক্ষতি ছিল না।
০২. শিল্পকলায়, চলায়, বলায় সবকিছুতেই ছন্দ
আমরা বলেছি যে, কবিতায় মিল থাক আর না-ই থাক, ছন্দ সর্বদা চাই। আগেও চাই, পরেও চাই। এখন কথা হচ্ছে, ছন্দবস্তুটা কী। ওটা আর কিছুই নয়, কবিতার শরীরে দোল লাগাবার কায়দা। তা নানান দোলায় কবিতার শরীরকে দোলানো যায়। ছন্দ তাই নানা রকমের।
কিন্তু ‘কবিতার ছন্দ’ নিয়ে আলোচনার আগে বরং মোটামুটিভাবে ছন্দ জিনিসটা নিয়েই কিছু বলা যাক।
ছন্দ বস্তুটা কী? আমরা যখন বলি, কমলের চেহারায় না আছে ছিরি না আছে ছাঁদ, তখন তার দ্বারা আমরা কী বোঝাতে চাই? এইটেই তো বোঝাতে চাই যে, কমলের চেহারা একে বিচ্ছিরি তায় বেঢপ। তাই না? (ছাঁদ কথাটা ছন্দ থেকেই এসেছে।) তাহলেই দেখা যাচ্ছে, যেমন কবিতার চেহারায়, তেমনি মানুষের চেহারাতে ও ছন্দ থাকা চাই।
মজা এই যে, ছন্দ না-থাকাটাও এক রকমের ছন্দ। কবিতায় না হােক, অন্য সব ব্যাপারে।
বড়ো রাস্তা দিয়ে ভীমবেগে এইমাত্র একটা লরি চলে গেল। তার ওই ভীমবেগে যাবার একটা ছন্দ আছে। লরি আসছে দেখবামাত্র দুটি লোক রাস্তা থেকে লম্ফ দিয়ে ফুটপাতে উঠে পড়লেন। তাদের ওই লম্ফ দিয়ে ফুটপাতে উঠবারও একটা ছন্দ আছে। ফুটপাথে উঠে তাদের এক জন, যেন কিছুই হয়নি এইভাবে, একটা বিড়ি ধরালেন। তার একটা ছন্দ আছে। অন্যজন, তখনও তার ভয় কাটেনি, ঝাড়া তিন মিনিট চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারও একটা ছন্দ আছে।
ছন্দ আছে সবকিছুতেই। নাতিবিখ্যাত কিন্তু অতিশক্তিমান এক বাঙালি প্রাবন্ধিকের লেখায় দুই ভদ্রলোকের প্রাতঃকালীন ভ্রমণের বর্ণনা দেখেছি। একজন মোটা, অন্যজন রোগা। একজন ঘোঁতঘোঁত করে হাঁটেন, অন্যজন পন্পন্ করে হাঁটেন। এই দুই রকমের হাঁটারই ছন্দ আছে।
আলোচনাকে এবারে কিছুটা উচ্চস্তরে উঠিয়ে আনি। রবীন্দ্ৰকাব্যের নায়িকা মাকে জিজ্ঞেস করছেন, “কী ছাদে কবরী বাঁধি লব আজ”। কেউ জানে না, শেষ পর্যন্ত তিনি কোন কায়দায় খোঁপা বেঁধেছিলেন। কিন্তু যে-কায়দাতেই বঁধুন, তাতে ছন্দ নিশ্চয়ই ছিল। ছন্দ যেমন টান-খোপাতে আছে, তেমনি এলো-খোপাতেও আছে। চুড়ো-খোঁপাতেও আছে, আবার লতানে খোঁপাতেও আছে।
ছন্দ আছে সর্বত্র। কুঁড়েঘরেও আছে, আবার আকাশ-ছোঁয়া অট্টালিকাতেও আছে। গৃহিণীর চাঁদপানা মুখেও আছে, আবার পাওনাদারের হাঁড়িপনা মুখেও আছে। চেয়ারে বসে ফাইল সই করাতেও আছে, আবার ঘাম ঝরিয়ে মোট বওয়াতেও আছে। আজ সকাল থেকে এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে। এর একটা ছন্দ আছে। আবার হাওয়া যখন মরে যাবে, এবং গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়বে না, তখন তারও একটা ছন্দ থাকবে। চোখের সামনে আমরা যা-কিছু দেখি, যা-কিছু শুনি, তার সবকিছুতেই- সমস্ত চলায়, সমস্ত বলায়, সব রকমের কাজে কিংবা অকাজে- ছন্দ রয়েছে। ছন্দ মানে এখানে ঢং কিংবা ডৌল কিংবা রীতি। সেটা কোথায় নেই?
এ-বাড়ির গিন্নি বলেন, ও-বাড়ির নতুন বউয়ের চলনে নেই। কিন্তু সেটা রাগের কথা। আসলে ও-বাড়ির নতুন বউয়ের চলনেও একটা ছন্দ আছে ঠিকই, তবে কিনা। এ-বাড়ির গিনির সেটা ভালো ঠেকছে না।
যা বলছিলুম। গাড়ি, বাড়ি, চলা, বলা, মাঠ, নদী, মেঘ, পাহাড়– সবকিছুরই একটা-না-একটা ছন্দ আছে। আছে কবিতারও। কিন্তু কবিতার ছন্দ বলতে যেকোনও রকমের একটা ছাদ বোঝায় না। সে-ও এক রকমের ছাদই, তবে কিনা তার নিজস্ব কতকগুলি নিয়মকানুন থাকে। মুখে আমরা যেসব কথা বলি, তাকে যদি সেই নিয়মকানুনের মধ্যে বেঁধে ফেলতে পারতুম, মুখের কথাও তাহলে কবিতা হয়ে উঠত।
বেঁধে ফেলার প্রস্তাব শূনেই বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, ছন্দ এক রকমের বন্ধন। কথাকে যা কিনা নিয়মের মধ্যে বঁধে। কিন্তু আর-এক দিক থেকে দেখতে গেলে, ঠিক বন্ধনও এটা নয়। রবীন্দ্রনাথ একে সেই দিক থেকেই দেখেছেন। তিনি বলেছেন, “এ কেবল বাইরে বাঁধন, অন্তরে মুক্তি। কথাকে তার জড়ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ।”
শুনে অনেকের ধাঁধা লাগতে পারে। বন্ধন কীভাবে মুক্তির পথ খুলে দেয়, সেই জটিল তত্ত্বটাকে সহজে বুঝিয়ে বলবার জন্যে রবীন্দ্রনাথ তাই সেতারের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। সুরকে ভালোভাবে মুক্তি দেবার জন্যেই তো সেতারের তারগুলিকে টান করে বেঁধে নিতে হয়। এ-ও সেই ব্যাপার। কথাকে। যদি না ছন্দে বাঁধি, তার অন্তরের সুর তাহলে ভালো করে মুক্তি পায় না।
ছন্দ আসলে কথার মধ্যে গতির তাড়া জাগিয়ে দেয়। আর এই গতির তাড়া জেগে উঠলেই আমরা দেখতে পাব যে, এমনিতে যাকে হয়তো খুব সহজ কথা কথাগুলিও তখন আশ্চর্য এক রহস্যের ছোঁয়ায় কেমন যেন চঞ্চল হয়ে ওঠে।
একটা দৃষ্টান্ত দিই।
ধরা যাক, আমাদের বলবার কথাটা এই যে, সারাটা দিন যা হােক কোনওক্ৰমে কেটে গেছে, কিন্তু বিকেলটা আর কাটতে চাইছে না। এমন কথা তো আমরা ; কতদিনই বলি। বলবার সঙ্গে-সঙ্গেই তা ফুরিয়েও যায়। কিন্ত এই কথাটাকেই রবীন্দ্রনাথ যখন ছন্দে বেঁধে বলেছেন, তখন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে, বলবার পরেও তার রেশ ফুরিয়ে যাচ্ছে না। সামান্য ওই কয়েকটি কথার মধ্যেই উদাস একটি বেদনার গতি এমন আশ্চর্যভাবে সঞারিত হয়ে গিয়েছে যে, শব্দগুলিকে সেই গতিই যেন ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। শ্রোতার অন্তরে বারবার গুঞ্জরিত হয়ে উঠছে একটি শব্দমালা :
“সকল বেলা কাটিয়া গোল
বিকাল নাহি যায়।”
রবীন্দ্রনাথ, বলাই বাহুল্য, গদ্যেও এই কথাগুলিকে খুবই মর্মগ্রাহী করে বলতে পারতেন। কিন্তু ছন্দের বাঁধনে এইভাবে না বঁধলে, কথাগুলির মধ্যে একটি বেদনার গতিকে হয়তো এতটাই মোক্ষমভাবে জাগিয়ে তোলা যেত না। এ যেন কথার নেপথ্য থেকে একটি দীর্ঘশ্বাসও বেশ স্পষ্ট করে শুনতে পাওয়া গেল।
শুধু বেদনার কথা কেন, ফুর্তির কথাকেও ছন্দে বেঁধে চঞলি করে তোলা যায়। শুনে, শ্রোতার মনও হঠাৎ কেমন চনমান করে ওঠে।
কথা এই যে, ছন্দ এক রকমের নয়। আবার একই ছন্দের মূল কাঠামোর মধ্যে নানান রকমের বৈচিত্র্যের খেলা দেখানো যেতে পারে। সেটা অবশ্য পরের কথা। তার আগে মূল ছন্দগুলির পরিচয় জানা চাই।
০৩. বাংলা কবিতার তিন ছন্দ
রবিবার সকাল। আপিসের তাড়া নেই। চুপচাপ বিছানায় শুয়ে, চোখ বুজে, তাই ছন্দ-ভাবনায় মগ্ন হয়ে ছিলুম। ভাবছিলুম যে, বাংলা কবিতা মোটামুটি তিন রকমের ছন্দে লেখা হয় :
১) অক্ষরবৃত্ত ২) মাত্রাবৃত্ত ৩) স্বরবৃত্ত।
বাংলা ছন্দের এই নাম নিয়ে অবশ্য আপত্তি উঠেছে। আপত্তির যে কারণ নেই, তা-ও নয়। কিন্তু…
চিন্তায় বাধা পড়ল। অন্নচিন্তা চমৎকারা। সুতরাং চক্ষু বুজে কাব্যচিন্তায় মগ্ন হওয়া অসম্ভব। (আমি আগেই আভাস দিয়েছি যে, আমাদের বাড়িতে প্রত্যেকেই কবি। ইস্তক আমার ভৃত্যটিও, কাজ না করুক, চমৎকার ছড়া মেলায়।) কনের কাছে হঠাৎ ঝংকার উঠল :
কর্মের বেলায় ঢুঢু, শুধু নিদ্রা দাও!
ওঠো বাবু কুম্ভকৰ্ণ, বাজারেতে যাও।
গৃহিণীর কণ্ঠ! আমি যে ছন্দ নিয়ে চিন্তা করছি, তা তিনি বুঝতে পারেননি। ভেবেছেন, স্রেফ ফাঁকি দেবার জন্য মটকা মেরে শুয়ে আছি। বলা বাহুল্য, তাঁর বাক্যের মধ্যে যে একটা গঞ্জনার ব্যঞ্জনা ছিল, সেটা আমার আদপেই ভালো লাগেনি; কুম্ভকৰ্ণ সম্বোধনটা তো রীতিমতো আপত্তিকর মনে হল। তবু গুণগ্রাহী মানুষ বললেই তাঁর সহজাত কাব্যপ্রতিভায় আমি মুগ্ধ হলুম।
বিছানা ছেড়ে তক্ষুনি অবশ্য উঠলুম না। কিন্তু শুয়ে থাকবারই-বা উপায় কী। খানিক বাদেই আমার আট বছরের নাতিটি এসে চেঁচাতে লাগল। :
সকলে ডেকে ডেকে হদ হল যে,
এক্ষুনি ওঠে, যাও খাদ্যের খোঁজে।
এর পরে আর শূয়ে থাকা চলে না। থলি নিয়ে বাজারের পথে রওনা হতে হল। ফিরতি পথে একবার মুদির দোকানে যাবার দরকার ছিল। কিন্তু যাওয়া হল না। না-যাবার হেতুটা অতিশয় প্রাঞ্জল। গত মাসের বিল অদ্যাবধি শোধ করা হয়নি, এবং আমি শ্ৰীকবিকঙ্কণ সরখেল যে একজন পুরোদস্তুর কবি, এই কথাটি বিলক্ষণ জানা সত্ত্বেও গতকাল মুদি আমাকে ধারে এক কিলো বাদামতেল দিতে আপত্তি করেছিল। শুধু তা-ই নয়, তার বিল আপাতত মেটানো হবে না। শুনেই সর্বসমক্ষে সে আমার তেলের বোয়মটা ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিল, “যান যান মশাই, কবিকে তেল দেওয়া আমার কৰ্ম্ম নয়।”
কথাটা মনে পড়ে যেতেই মুদির দোকানের সান্নিধ্য বর্জন করে আমি অন্য পথে বাড়ি ফিরলুম। ফিরেই বুঝলুম, বাড়িতে তেল না থাক, ঘি আছে, এবং প্রাতরাশের জন্যে লুচি ভাজবার আয়োজন হচ্ছে। রাঁধুনি বামনিকে তো আমার কন্যার উদ্দেশে স্পষ্টই বলতে শোনা গেল :
দিদি আসুন, ময়দা ঠাসুন,
আজকে রবিবার।
মোহনভোগের সঙ্গে লুচি,
জমবে চমৎকার!
শুনে আমি যৎপরোনাস্তি প্রীত হলুম। তার কারণ নেহাত এই নয় যে, বাড়িতে লুচি হলে আমিও তার ভাগ পাব। বলা বাহুল্য, সেটাও একটা কারণ বটে, তবে আমার আনন্দের প্রধান কারণটা এই যে, আজ সকালে ঘুম ভাঙবার পর, মাত্ৰ ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই, বাংলা কবিতার প্রধান তিনটি ছন্দের নমুনা আমি পেয়ে গিয়েছি। এখন দেখা যাক, একই কথাকে নানান রকমের ছন্দে আমরা বাঁধতে পারি। কিনা। না না, আর ওই হাট-বাজার-তেল-ঘি-কয়লা-কেরোসিন নয়; আসুন, কবিদের যা কিনা খুবই প্রিয় প্রসঙ্গ, সেই পূর্ণিমার চাঁদ নিয়ে কিছু লিখি। ধরা যাক, আমাদের বলবার কথাটা এই যে, শ্রাবণ মাসের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে, আর সেই গোল চাদকে একটা সোনার থালার মতো দেখাচ্ছে। এখন এই কথাগুলিকে যদি ছন্দে বেঁধে বলতে হয়, তো আমরা কীভাবে বলব? প্রথমত এইভাবে বলতে পারি :
দ্যাখো ওই পূৰ্ণচন্দ্র শ্রাবণ-আকাশে,
স্বর্ণের পত্রটি যেন শূন্য পরে ভাসে।
এ হল অক্ষরবৃত্ত ছন্দ (পরবর্তীকালে শ্ৰীপ্ৰবোধচন্দ্র সেন মহাশয় এর নাম দিয়েছেন মিশ্রকলাবৃত্ত’। আর শ্ৰীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই ছন্দকে বলেন ‘তানপ্রধান’) শ্রাবণ মাসের মেঘাচ্ছন্ন আকাশে পূৰ্ণচন্দ্ৰ আদৌ দেখা সম্ভব কি না, এক্ষুনি সেই কুটকচালে তর্ক তুলে লাভ নেই; তার চাইতে বরং ভাবা যাক, অক্ষরবৃত্ত ছন্দের মধ্যে আমাদের বক্তব্যের সুর কি ঠিকমতো বেজে উঠল? যদি মনে হয়, বাজেনি, তো এই একই বস্তুব্যকে আমরা অন্য ছাদেও বাঁধতে পারি। ছন্দ পালটে লিখতে পারি। :
আকাশে ছড়ায় পূর্ণচাঁদের বাণী
শ্রাবণ-রাত্রি হাসে;
দেখে মনে হয়, স্বৰ্ণপাত্ৰখানি
নীল সমুদ্রে ভাসে।
এ হল মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। (শ্ৰীপ্ৰবোধচন্দ্র সেন এর নতুন নাম দিয়েছেন ‘কলাবৃত্ত’। আর শ্ৰীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় একেই বলেন ‘ধ্বনিপ্রধান’ ছন্দ।) লাইনগুলি আরএক বার পড়ে দেখুন; ঠিক বুঝতে পারবেন যে, এর দোলাটা একেবারে অন্য রকমের। এতক্ষণ যেন শান্ত জলে নৌকো চলছিল, এবার ঢেউয়ের দোলায় উঠছেনামছে। এই দোলাটা কি ভালো লাগছে। আপনাদের? নাকি মনে হচ্ছে যে, এ-ও যেন ঠিক মনের মতো হল না? বেশ তো, তাহলে আসুন, আমাদের কথাগুলিকে এবারে আর-এক রকমের ছন্দে দুলিয়ে দেওয়া যাক। লেখা যাক :
দ্যাখো দ্যাখে আজকে যেন
শ্রাবণ-পূর্ণিমায়
সোনার থালা আটকে আছে
নীল আকাশের গায়।
এ হল স্বরবৃত্ত ছন্দ। (শ্ৰীপ্ৰবোধচন্দ্র সেন এই ছন্দকে এখন দলবৃত্ত’ বলেন। শ্ৰীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বলেন ‘শ্বাসাঘাতপ্রধান’ ছন্দ।)
দেখা যাচ্ছে, একই কথাকে আমরা তিন রকমের ছন্দে বাঁধিলুম। নমুনা তিনটিকে এবারে পাশাপাশি মিলিয়ে নিন, তাহলেই এদের পার্থক্যটা বেশ স্পষ্ট করে ধরা পড়বে। পার্থক্য এদের মাত্রায়, পার্থক্য এদের ঝোকে, পার্থক্য এদের পর্ব-বিন্যাসে। মাত্রা, ঝোক, পর্ব-এসব কথা নতুন ঠেকছে তো? ভয় নেই, ছন্দের আলোচনা আর-একটু এগোলেই এসব জল হয়ে যাবে।
০৪. অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রকলাবৃত্ত বা তানপ্রধান ছন্দ
আপনারা ইতিমধ্যে জেনে নিয়েছেন যে, বাংলা কবিতার ছন্দ মোটামুটি তিন রকমের। অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্ত। শুধু যে তাদের নামই আপনারা জেনেছেন তা নয়, চেহারাও দেখেছেন। কিন্তু সে-দেখা নেহাতই এক লহমার। তার উপরে নির্ভর করে কি আর কবিতা লিখতে বসে যাওয়া যায়? তা ছাড়া আমরা সেকেলে মানুষ। আমরা পাত্রী দেখতুম খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। মেয়ের দাঁত উঁচু কি না, খড়ম-পা কি না, হাত কাঠি-কাঠি কি না, খোঁপা খুলে দিলে চুলের ঢাল কোমর ছাড়িয়ে নীচে নামে কি না, হাসলে পরে মুক্তো না ঝাবুক, গালে টোল পড়ে কি না, সব দিকে আমাদের নজর থাকত। এমনকি, “একবার হাঁটো তো মা’, বলে এক বারের জায়গায় পাঁচবার হাঁটিয়ে নিয়ে তার চলনের ভঙ্গিটিও আমরা দেখে নিতুম। সুতরাং ছন্দকেই বা আমরা অল্পে ছাড়ব কেন? আসুন, সেকালে যেভাবে পােত্রী দেখা হত, ছন্দকেও সেইভাবে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখা যাক।
প্রথমেই দেখব অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে। শুধু যে দেখব তা নয়, তার কুলশীলগাঁঞিগোত্ৰমেল ইত্যাদিরও একটু-আধটু খোঁজ নেব। এসব ব্যাপারে অল্পে তুষ্ট হওয়াটা কোনও কাজের কথা নয়।
নাম আছে। যথা, অক্ষরমাত্রিক, বর্ণমাত্রিক ইত্যাদি। অক্ষরবৃত্ত নামটা শ্ৰীপ্ৰবোধচন্দ্র সেনের দেওয়া। তা ছাড়া তিনি একে যৌগিক ছন্দও বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ একে কখনও বলেছেন সাধু ছন্দ, কখনও বলেছেন পয়ারজাতীয়। আর শ্ৰীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। একে বলেন তানপ্রধান ছন্দ। শ্ৰীপ্ৰবোধচন্দ্র সেনও মনে করেন যে, অক্ষরবৃত্ত নামের মধ্যে এই ছন্দের চরিত্র-পরিচয় ঠিক ধরা পড়েনি। সেই কারণেই পরবর্তীকালে অক্ষরবৃত্ত নামটি তিনি বর্জন করেছেন, এবং এর নতুন নাম দিয়েছেন মিশ্রকলাবৃত্ত। কিন্তু নামাবলি নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। নামের মূল্য নামমাত্র। আর তা ছাড়া, মহাকবি শেকসপিয়র তো বলেই দিয়েছেন, গোলাপকে যে-নামেই ডাকে, তার গন্ধের তাতে তারতম্য ঘটবে না। সব ব্যাপারেই তা-ই। আর তাই, অন্যান্য নামের গন্ডগোলে না। ঢুকে আপাতত ওই অক্ষরবৃত্ত নামটাই ব্যবহার করা যাক। তাতে কাজের অনেক সুবিধে হবে।
এইখানে বলে রাখি, বয়সের বিচারে অক্ষরবৃত্ত খুবই বনেদি ছন্দ। রবীন্দ্রনাথের আগে পর্যন্ত, এমনকি রবীন্দ্ৰকাব্যেরও সূচনাপর্বে, বাংলা কবিতা প্রধানত অক্ষরবৃত্তেই লেখা হয়েছে। কিন্তু এর থেকে আবার এমন কথা কেউ যেন ভেবে না বসেন যে, অক্ষরবৃত্ত নেহাতই সাবেক-কালের ছন্দ, একালে আর তার চলন কিংবা কদর নেই। না, তা নয়। বরং সত্যি বলতে কী, হাল আমলের কবিতায় দেখছি অক্ষরবৃত্ত আবার নতুন করে আসর। জাঁকিয়ে বসেছে।
অক্ষরবৃত্তের লক্ষণ কী? লক্ষণ মোটামুটি এই যে, এ-ছন্দে যত অক্ষর বা বর্ণ, তত মাত্রা। অর্থাৎ কিনা প্রতিটি অক্ষরই এখানে একটি মাত্রার মর্যাদা পেয়ে থাকে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :
১) গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর
২) দ্যাখো চারু যুগ্মভুবু ললাট প্রসর
৩) শ্যামল সুন্দর প্রভু কমললোচন
৪) গুণ হৈয়া দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায়
৫) নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
৬) পোড়া প্রণয়ের বুঝি জরামৃত্যু নাই
৭) কঁপে তারা কঁপে উরু, গুরুগুরু করি
৮) চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির
৯) ওষ্ঠ্যাধরে বিম্বফল লজ্জা নাহি পায়
১০) বঙ্গভূমি পদে দলে তুরস্ক সোয়ার।
বাংলা কাব্যের মহাসমুদ্রে ড়ুব দিয়ে, যেমন- যেমন হাতে মিলল, দশ-দশটি পঙক্তি তুলে নিয়ে এলুম। এদের প্রত্যেকের ছন্দ অক্ষরবৃত্ত। প্রত্যেক পঙক্তিতে অক্ষরের সংখ্যাও যেমন চোদো, মাত্রার সংখ্যাও তেমনি চোদো। তার মানে এই নয় যে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কবিতার এক-একটি পঙক্তিতে ঠিক চোদ্দেটো অক্ষরই থাকতে হবে। না, তা নয়। তবে, অক্ষরের সংখ্যা বাড়লে কিংবা কমে গেলে মাত্রার সংখ্যাও সেইসঙ্গে বাড়বে কিংবা কমে যাবে। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শেষ পর্যন্ত দেখা যাবে, পঙক্তির মাপ বাড়ুক, কিংবা কামুক, অক্ষর আর মাত্রার সংখ্যা সমান-সমানই রইল।
কথা এই যে, অক্ষরবৃত্তের পঙক্তিকে বাড়ানো-কমানো যায় ঠিকই, কিন্তু নেহাতই খেয়ালখুশিমতো বাড়ানো-কমানো যায় না। অর্থাৎ হ্রাসবৃদ্ধির একটা কানুন আছে, সেই কানুন মেনে তবেই লাইনটাকে বাড়ানো-কমানো চলে। কিন্তু সে-কথায় একটু বাদে ঢুকব। তার আগে জানা দরকার, এত যে মাত্রা-মাত্রা করছি, সেই মাত্ৰা জিনিসটা কী?
আমরা কথায় বলি, অমুক লোকটার মাত্রাজ্ঞান আছে, তমুক লোকটার নেই। ইংরেজিতে একেই বলে সেনস অব প্রোপোরশান। প্রোপোরশানের বাংলা অর্থ অনুপাত। মাত্রা বলতে কি তাহলে অনুপাত বুঝব?
না, মহাশয়, কবিতায় ঠিক এই অর্থে ‘মাত্ৰা’ কথাটার ব্যবহার হয় না। তবে কোন অর্থে হয়?
জানি, আমার কপালে দুঃখ আছে, ছান্দসিকদের কাছে ধমক আমাকে খেতেই হবে। কিন্তু উপায় কী, বিজ্ঞজনেরা যতই চোখ রাঙিয়ে আমাকে ভৎসনা করুন, মাত্রা বোঝাতে গিয়ে কোনও গুরুগম্ভীর জটিল ব্যাখ্যার অবতারণা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আমার ক্লাস খুলেছি নতুন পড়ুয়াদের নিয়ে, ‘ব্যাঘ্র মানে শার্দুল’ শুনলেই তাঁরা ঘাবড়ে গিয়ে ক্লাস ছেড়ে পালাবেন। তাই, কিছুটা ত্রুটির ঝুঁকি নিয়েও, খুব সহজ করে ব্যাপারটা তাদের বুঝিয়ে দিতে চাই। আপাতত, প্ৰবোধচন্দ্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এইটুকু বুঝলেই তাদের কাজ চলবে যে, “যার দ্বারা কোনো-কিছুর পরিমাপ করা যায়”, তাকেই আমরা মাত্রা বলে থাকি। প্রবোধচন্দ্র বলেছেন, “মাত্রা মানে পরিমাপক”, অর্থাৎ ইউনিট অব মেজার। এখন, বলা বাহুল্য, বস্তুভেদে ওই পরিমাপের ইউনিটও আলাদা হতে পারে, হয়ে থাকে। জল মাপবার ইউনিট যদি ফোঁটা, তো কাপড় মাপাবার ইউনিট হয়তো মিটার কিংবা গজ। ইউনিটের এই বিভিন্নতার ব্যাপারটা প্ৰবোধচন্দ্র নিজেই ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়ে বলেছেন যে, ছন্দের রীতিভেদেও মাত্রা বিভিন্ন হয়। যাই হোক, আমার পড়ুয়ারা মোটামুটি এইটুকু জেনে রাখুন যে, কবিতার এক-একটি পঙক্তির মধ্যে যে ধ্বনিপ্রবাহ থাকে, এবং তাকে উচ্চারণ করার জন্য মোট যে-সময় আমরা নিয়ে থাকি, সেই উচ্চারণকালের ক্ষুদ্রতম এক-একটা অংশই হল মাত্রা। প্ৰবোধচন্দ্র তারই নাম দিয়েছেন “কল”। কিলা’ মানে এখানে অংশ। যেমন ষোলো-কলায় চাঁদ পূর্ণ হয়, তেমনি কলা কিংবা মাত্রার সমষ্টি দিয়ে তৈরি হয় পূর্ণ এক-একটি পঙক্তির উচ্চারণকাল।
ব্যাপারটাকে এবারে হাতে-কলমে পরীক্ষা করে দেখা যাক। ‘গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সবার উপর’— এই লাইনটিকে একবার চেচিয়ে উচ্চারণ করুন তো। করেছেন? করতে যে-সময় লাগল, সেই উচ্চারণকাল মোট চোদ্দোটি মাত্রার সমষ্টি। অর্থাৎ এই মাত্রাগুলি হচ্ছে লাইনটির উচ্চারণকালের ক্ষুদ্রতম এক-একটি অংশ। মোট মাত্রা এখানে চোদ্দে! আবার লাইনটির মোট অক্ষরের সংখ্যাও তা-ই। কিন্তু অক্ষর আর মাত্রাকে এইভাবে তুল্যমূল্য করে দেখার একটা বিপদ আছে। যথা “ঐ দৃশ্যত একটিই অক্ষর বটে, কিন্তু তাকে ভেঙে “ওই লিখলেই অক্ষরের সংখ্যা দুয়ে গিয়ে দাঁড়ায়। অথচ “ঐ” আর ওইয়ের উচ্চারণ তো একই। ফলে, অক্ষরবৃত্তে কেউ যদি “ঐ” লিখে ওই একাক্ষর দিয়ে দু-মাত্রার কাজ চালান, তাকে দোষ দেওয়া যাবে না। ‘বউ’ আর ‘বৌ’য়ের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার। “হাওয়া’, “পাওয়া’, ‘খাওয়া”, ইত্যাদির বেলাতেও অক্ষর আর মাত্রাকে সংখ্যার ব্যাপারে। তুল্যমূল্য করে দেখবার উপায় নেই। ওসব শব্দের ‘ওয়া’-অংশে যদিও দুটি অক্ষর, কার্যত সেই অক্ষর দুটি কিন্তু এক মাত্রার বেশি দাম পায় না।]
তা ছাড়া আমরা চার-অক্ষরের সমবায়ে লিখি ‘তোমরই’ ‘আমারই’ কিন্তু উচ্চারণ করি ‘তোমারি’ ‘আমারি’; তিন অক্ষরের সমবায়ে লিখি ‘সবই’, কিন্তু উচ্চারণ করি ‘সবি’— ধ্বনির আয়তনের বিচারে দু-অক্ষরের ছবির সঙ্গে তার ফারাক থাকে না। পরে আমরা দেখিয়ে দেব যে, অক্ষর দেখে মাত্রা গুনতে গেলে আরও নানা বিপদ ঘটতে পারে। আপাতত এইটুকু জেনে রাখুন যে, ছন্দের ব্যাপারে। আসলে ধ্বনিটাই প্রধান কথা, অক্ষরটা নয়। তবু ছন্দশিক্ষার প্রাথমিক পর্বে (অর্থাৎ মাত্রা ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় ঘটেনি, তখন) অক্ষরের ভিত্তিতে ছন্দ চেনাবার চেষ্টা করেছি। এই জন্যে যে, নতুন পড়ুয়ার তাতে সুবিধে হয়। সেই প্রাথমিক পর্ব তো চুকেছে; এখন বলি, অক্ষরের উপর চোখ না-রেখে ধ্বনির দিকে কান রাখুন। ছন্দনির্ণয় আর মাত্ৰা-বিচার তাতেই নির্ভুল হবে।
এবারে তাহলে লাইনের দৈর্ঘ্যের হ্রাসবৃদ্ধির প্রসঙ্গে যাওয়া যাক। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের নমুনা দিতে গিয়ে ইতিপূর্বে আমি যেসব লাইন তুল দিয়েছিলুম, তার প্রত্যেকটিই চোদ্দো মাত্রার লাইন। এবারে বলি, এ-ছন্দে ছ-মাত্রার লাইন লেখা যায়, দশ মাত্রার লাইন লেখা যায়, চোদো মাত্রার লাইন লেখা যায়, আঠারো মাত্রার লাইন লেখা যায়, বাইশ মাত্রার লাইন লেখা যায়, ছাব্বিশ মাত্রার লাইন লেখা যায়এমন কী, তিরিশ মাত্রার লাইনও আমি দেখেছি। তার বেশি বাড়াতে হলে চৌত্রিশ মাত্রায় যেতে হয়। কেউ গিয়েছেন বলে আমি জানিনে।
হ্রাসবৃদ্ধির কানুনটা তাহলে কী? এখনও সেটা বুঝতে পারেননি? ছয়, দশ, চোদ্দো, আঠারো, বাইশ— মাত্রার সংখ্যা কীভাবে বাড়ছে দেখুন। লোকে বলে চড় চড় করে বেড়ে যাওয়া, এখানে চারচার করে বাড়ছে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের চাল আসলে চার মাত্রার চাল। মূলে রয়েছে চার। তার সঙ্গে, কিংবা চারের যে-কোেনও গুণিতকের সঙ্গে (অর্থাৎ চার-দুগুণে আটের সঙ্গে, কিংবা তিন-চারে বারোর সঙ্গে, কিংবা চার-চারে ষোলোর সঙ্গে, কিংবা চার-পাঁচে কুড়ির সঙ্গে) দুই যোগ করলে যে-সংখ্যাটা মিলবে, তত সংখ্যার মাত্ৰা দিয়েই অক্ষরবৃত্তের লাইন তৈরি করা যায়।
দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :
লক্ষ ঢাকঢোল
বাজিছে হোথায়।
চক্ষু হয় গোল,
লোকে মূৰ্ছা যায়।
এ হল ৪+২=৬ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত। এত ছোটো মাপে যদি মন না ওঠে, তো এর সঙ্গে আরও চার মাত্রা জুড়ে দিয়ে ৪+৪+২=১০ মাত্রার লাইনও আমরা বানাতে পারি। ব্যাপারটা সেক্ষেত্রে এই রকমের দাঁড়াবে :
ওই শোনো প্ৰচণ্ড দাপটে
লক্ষ ঢাকঢোল বেজে যায়।
ভক্তের আসর জমে ওঠে
ঘন-ঘন-পতনে মূৰ্ছায়।
আরও বাড়াতে চান? বেশ তো বাড়ান না, ফি-লাইনে আরও চারটি করে মাত্রা জুড়ে দিন। দিলে হয়তো এই রকমের একটা চেহারা মিলতে পারে :
ওই শোনো সাড়ম্বরে প্রচণ্ড দাপটে
মহোল্লাসে লক্ষ লক্ষ ঢোল বেজে যায়।
গর্জনে-হুংকারে ওই সভা জমে ওঠে
ভক্তদের ঘন-ঘন পতনে মূর্ছায়।
এ হল ৪+৪+৪+২=১৪ মাত্রার অক্ষরবৃত্ত।
ঠিক এইভাবেই আমরা আরও চারটি মাত্রা বাড়াতে পারি, এবং চোদ্দের জায়গায় আঠারো-মাত্রার (৪+৪+৪+৪+২-১৮) লাইন বানাতে পারি। কিন্ত তার আর দরকার কী?
কথা হচ্ছে, যে-ছন্দের চাল মূলত চার মাত্রার, তার ফি-লাইনে ওই বাড়তি দুমাত্রা যোগ করতে হয় কেন? বলি।
কবিতা পড়তে-পড়তে মাঝে-মাঝে একটু দম ফেলবার অবকাশ চাই। একটানা তো ছোটো যায় না; ছুটতে-ছুটিতে খানিক-খানিক দাঁড়িয়ে নেওয়া চাই। ওই দু-মাত্রা সেই ক্ষণিক-বিরতির ব্যবস্থা করেছে। ওদের যদি না জুড়ে দেওয়া হত, লাইনের শেষে তাহলে দাঁড়াবার জায়গা পাওয়া যেত না। প্রথম লাইন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় লাইনের উপরে গিয়ে কুমড় খেয়ে পড়তে হত, দ্বিতীয় লাইন ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে-সঙ্গেই তৃতীয় লাইনের উপরে। এবং এইরকমই চলত, গোটা কবিতাটা যতক্ষণ না একেবারে ফুরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তেমনভাবে তো আমরা কবিতা পড়তে পারিনে। পড়িমরি ছুটি লাগিয়ে কবিতা পড়া যায় না; আর-কিছু না হোক, দম ফেলবার ফুরসতটুকু চাই। সেই ফুরসতটুকুই মিলিয়ে দিচ্ছে ফি-লাইনের শেষে জুড়ে-দেওয়া ওই মাত্রা দুটি। ওরা যদি না-থাকত, কবিতা পড়া তাহলে যে কী ঘোড়দৌড়ের ব্যাপার হত, নীচের কয়েকটি লাইন পড়লেই তা বুঝতে পারবেন :
বাজে লক্ষ ঢাকঢোল
চতুর্দিকে হট্টগোল
আর সহ্য হয় কত,
প্ৰাণ হল ওষ্ঠাগত।
ভক্তেরা বিষম খান,
দলে-দলে মূৰ্ছা যান।
বুঝতেই পারছেন, কী হুলুস্থুলু ব্যাপার! বাড়তি দুমাত্রাকে ছোট দিয়ে শুধুই চারের চালের উপরে নির্ভর করে এই ছত্র-কটি দাঁড়িয়ে আছে। তার ফল হয়েছে এই যে, দাঁড়ি-কমা থাকা সত্ত্বেও লাইনের শেষে দাঁড়ানো যাচ্ছে না; ছন্দের তাড়না এতই প্রবল হয়ে উঠেছে যে, পাঠককে সে লাইন থেকে লাইনে ছুটিয়ে মারছে। এই ঘোড়দৌড়কে ঠেকাবার জন্যেই লাইনে-লাইনে বাড়তি দুটি মাত্রা জুড়ে দেওয়া দরকার।
কবিতার আলোচনায় ঘোড়দৌড় কথাটা যদি আপত্তিকর মনে হয়, তবে না-হয়। পাখির উপমা দেব। বাড়তি দু-মাত্রা যখন থাকে না, পাখিকে তখন ক্ৰমাগত উড়তে হয়। আর লাইনের শেষে ওই দু-মাত্ৰা আশ্রয় থাকলে সেইটোকে ধরে সে একটুক্ষণের জন্যে জিরিয়ে নিতে পারে। কিংবা বলি, চারের চালের কবিতা যেন একটা বহতা নদী। ফি-লাইনের শেষের ওই দু-মাত্রা তাতে বিয়ার মতন ভাসছে। সাতার কাটতে-কাটিতে আমরা ওই বয়াকে গিয়ে ধরছি– ব্যাপারটা অনেকটা এই রকমের।
মজা এই যে, লাইনটাকে যখন একসঙ্গে দেখি, তখন গোটা লাইনের বিন্যাসের মধ্যে ওই বাড়তি মাত্রা দুটি এমন চমৎকারভাবে নিজেদের ঢেকে রাখে যে, ওরা যে আলাদা, তা ঠিক ধরাও পড়ে না। বিশেষ করে, ছয় কি দশের বৃত্ত ছাড়িয়ে আমরা যখন চোদ্দো মাত্রায় গিয়ে পৌঁছেই, অতিরিক্ত ওই দু-মাত্রাকে তখন ছন্দের মূল চালেরই অঙ্গ বলে মনে হয়। তার হেতুটা আর কিছুই নয়, লাইনের টুকরো-টুকরো অংশের যেমন ছোটো মাপের চাল থাকে, তেমনি গোটা লাইনটারও আবার একটা বড়ো মাপের চাল থাকে। ছােটো মাপের চালের দিকে যখন তাকাই, বাড়তি দুমাত্রাকে তখন আলাদা করে দেখতে পাই; কিন্তু বড়ো মাপের চালের দিকে ৩াকালে আর দেখতে পাইনে। তার কারণ এই যে, ছোটো চালটা বাড়তি দু-মাত্রাকে দূরে ঠেলে দেয়; বড়ো চাল তাকে নিজের মধ্যে টেনে আনে। হাতেকলমে বুঝিয়ে দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে–
ওই শোনো সাড়ম্বরে প্রচণ্ড দাপটে
মহোল্লাসে লক্ষ লক্ষ ঢোল বেজে যায়।
এই-যে দুটি লাইন, ছোটো চালের হিসেব মেনে যদি এদের ভাগ করে ফেলি, ব্যাপারটা তাহলে এইরকম দাঁড়াবে–
ওই শোনো/সাড়ম্বরে/প্রচণ্ড দা/পটে
মহোল্লাসে/লক্ষ লক্ষ/ঢোল বেজে/যায়।
এইভাবে ভাগ করে দেখতে পাচ্ছি, ফি-লাইনের এক-এক অংশে (এই অংশেরই অন্য নাম ‘পর্ব) চারটি করে মাত্রা পড়ছে, আর লাইনের প্রান্তে পড়ে থাকছে সেই বাড়তি দু-মাত্রা।
কিন্তু কবিতা পড়বার সময়ে তো ঠিক এই রকমের ছোটো চালে পা ফেলে আমরা পড়িনে। আর-একটু লম্বা চালে এইরকমে পড়ি—
ওই শোনো সাড়ম্বরে/প্রচণ্ড দাপটে
মহোল্লাসে লক্ষ লক্ষ/ঢোল বেজে যায়।
তখন মনে হয়, লাইনগুলি যেন দুটি ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আট মাত্রা, দ্বিতীয় ভাগে ছ-মাত্রা।
অক্ষরবৃত্তের আঠারো মাত্রার লাইনকেও এই বড়ো চালে ভাঙা যায়। ভাঙলে তার প্রথম ভাগে পড়বে আট মাত্রা, দ্বিতীয় ভাগে দশ মাত্রা।
মোটকথা, বড়ো চালে যখন চলি, লাইনের শেষের বাড়তি দু-মাত্রাকে তখন আর আলাদা করে ধরতে পারিনে। বাইরের লোক হয়েও সে তখন ছন্দের ভিতরে এসে ঢুকে পড়ে; বৈঠকখানায় দাঁড়িয়ে না থেকে অন্দরমহলে এসে আপনার লোক হয়ে যায়।
অক্ষরবৃত্তের চেহারা দেখলুম, চরিত্রের খোঁজখবর নিলুম, চালচলনেরও একটা আন্দাজ পাওয়া গেল। কিন্তু মোদী কথাটা বোঝা গেল কি?
আলোচনার সুবিধের জন্যে আবার চলুন ধ্বনিকে ছেড়ে অক্ষরের কাছে ফিরে যাই। আমি বলেছি, এ-ছন্দের এক-এক লাইনে অক্ষর যত, মাত্ৰাও তত। এইটেই সাধারণ নিয়ম। এর যে ব্যতিক্রম হয় না, তা নয়। বিস্তর হয়। তার কারণ, ধ্বনি সর্বদা অক্ষরের আঁচল ধরে চলে না। কিন্তু ব্যতিক্রমের কথা এখুনি বলতে চাইনে। পরে বলব। অক্ষরের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও অনেকসময়ে ধ্বনির পরিসর কেন বাড়ে না, এবং মাত্রার যোগফলও তার দরুন। একটা নির্দিষ্ট হিসেবের মধ্যেই থেকে গিয়ে কীভাবে লাইনের ভারসাম্যকে ধরে রাখে, তা-ও বলব। আপাতত শুধু সাধারণ নিয়ম নিয়েই আলোচনা করা যাক।
সাধারণ নিয়মটা এই যে, অক্ষর আর মাত্রার সংখ্যা এতে সমান-সমান। তার চাইতেও জরুরি কথা, অক্ষর আর যুক্তাক্ষর এ-ছন্দে তুল্যমূল্য; অক্ষরবৃত্তের লাইনে যদি যুক্তাক্ষর-সংবলিত শব্দ ঠেসেও বসান, মাত্ৰা-সংখ্যার তবু ইতরবিশেষ হবে না। লাইনের ওজন তাতে বাড়বে বটে, কিন্তু দৈর্ঘ্য তার ফলে মাত্রার সীমা ছাড়াবে না। অর্থাৎ ছন্দও বে-লাইন হবে না।
দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। প্রথমে আসুন দশ-মাত্রার অক্ষরবৃত্ত নিয়ে পরীক্ষা করে দেখি।
নিশীথিনী ভোর হয়ে আসে
আলো ফোটে পুবের আকাশে।
দশ-মাত্রার অক্ষরবৃত্তে লেখা এই যে দুটি লাইন, এর মধ্যে যুক্তাক্ষর একটিও দেওয়া হয়নি। দিয়ে দেখা যাক কী হয়।
আমারাত্রি ভোর হয়ে আসে
আলো ফোটে পূর্বের আকাশে।
কী হল? কিছুই হল না। এক-এক লাইনে একটি করে যুক্তাক্ষর ঢোকালুম, কিন্ত অক্ষরবৃত্ত তাকে দিব্যি গিলে নিল। দশ-মাত্রা দশ-মাত্ৰাই আছে, এগারো হয়ে গিয়ে ছন্দপতন ঘটায়নি।
আরও কিছু ভার তাহলে চাপানো যাক :
অন্ধকার সাঙ্গ হয়ে আসে
রক্ত-আভা পূর্বের আকাশে।
এক-এক লাইনে এবারে দু-দুটো করে যুক্তাক্ষর বসালুম। কিন্তু তাতেই-বা কী হল? মাত্রা সেই দশেই আটকে আছে।
ভার তাহলে আরও বাড়িয়ে দেখি।
কৃষ্ণরাত্রি সাঙ্গ হয়ে আসে
রক্তচ্ছটা পূর্বের আকাশে।
কিন্তু তাতেও কিছু ইতারবিশেষ হল না। ফি-লাইনে তিন-তিনটে যুক্তাক্ষরকে অক্লেশে গিলে নিয়ে দশ-মাত্রার অক্ষরবৃত্ত সেই দশ মাত্রাতেই দিব্যি দাঁড়িয়ে আছে।
দশ মাত্রায় যদি মন না। ওঠে তো চোদ্দো-মাত্রার লাইন নিয়ে পরীক্ষা করুন।
‘চলো ভাই মাঠে যাই বেড়াইয়া আসি’
বাল্যে-পাঠ্য একটি বিখ্যাত কবিতার এটি প্রথম লাইন। এর ছন্দ অক্ষরবৃত্ত। অক্ষরের সংখ্যা এখানে চোদ্দো, মাত্রার সংখ্যাও তা-ই। যুক্তাক্ষর এতে একটিও নেই। কিন্তু থাকলেও তার ফলে মাত্রার সংখ্যা বেড়ে যেত না। প্রমাণ দিচ্ছি :
চলো বন্ধু মাঠে যাই বেড়াইয়া আসি
ভাইকে তাড়িয়ে দিয়ে আমরা বন্ধুকে এনে ঘরে ঢোকালুম। ফলে একটি যুক্তাক্ষরও এল। কিন্তু মাত্রার সংখ্যা। তবু চোদ্দো-ই। এবার দেখুন :
চলো বন্ধু মুক্ত-মাঠে বেড়াইয়া আসি।
দু-দুটি যুক্তাক্ষর ঢুকেছে। কিন্তু মাত্রার সংখ্যা। তবু বাড়েনি। অতঃপর :
চলো বন্ধু সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে মাঠে যাই।
অর্থাৎ তিন-তিনটে যুক্তাক্ষর ঢুকল। কিন্তু মাত্রার সংখ্যা। তবু সেই চোদ্দেই, তার বেশি নয়। কিংবা :
সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে নিয়ে মুক্ত-মাঠে চলো
এবারে চার-চারটে যুক্তাক্ষর। কিন্ত লাইনের মাত্ৰাসংখ্যা। তবু সেই চোদ্দোতেই ঠেকে আছে, এক ক্ৰান্তিও বাড়েনি।
যুক্তাক্ষরের সংখ্যা এইভাবে আরও বাড়ানো যায়। কত যে বাড়ানো যায়, সেটা বোঝাতে গিয়ে রবীন্দ্ৰনাথ লিখেছিলেন :
‘দুৰ্দান্ত পণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত’
যুক্তাক্ষর এখানে গিসগিস করছে। কিন্তু মাত্রার সংখ্যা তবু সেই চোদ্দে তো চোদ্দেই, ওজনে-ভারী এতগুলি যুক্তাক্ষরকে বক্ষে ধারণ করেও অক্ষরবৃত্তের এই লাইনটি তবু সেই চোদ্দো-মাত্রাতেই ঠেকে আছে।
অক্ষরবৃত্ত যেন সৰ্বংসহা বসুন্ধরার মতো। তার উপরে যতই-না কেন ভার চাপানো হোক, মুখ বুজে। সে সহ্য করবে। তার জন্যে সে বাড়তি-মাত্রার মাশুল চাইবে না; যেমন অন্যান্য অক্ষরকে, তেমনি যুক্তাক্ষরকেও সে মাত্র এক-মাত্রার মূল্যেই বহন করে। তার দৃষ্টান্তও আমরা দিয়েছি।
কথা এই যে, দুটি অক্ষর যদি দৃশ্যত পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত না-হয়েও শ্রবণের বিচারে পরস্পরের সঙেগ জুড়ে যায়, তো অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কবিতায় সেই অক্ষরদুটিকে- দৃশ্যত তারা যুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও- মাত্র একমাত্রার মাশুল দিয়েই তারিয়ে দেওয়া যায় কি? যায় না, এমন কথা কেমন করে বলব? কবিরা অনেক ক্ষেত্রে দিব্যি তারিয়ে দেন। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :
চকর্পূর-সুবাসে জল ভরপুর হয়েছে
এই যে লাইনটি, এর মধ্যে ‘কর্পূর’ শব্দটি যে তিন-মাত্রা, তাতে সন্দেহ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, ‘ভরপুর’ও কি তা-ই?
হ্যাঁ, তা-ই। তার কারণ, ‘ভরপুর’-এর রিপু দৃশ্যত যুক্ত নয় বটে, কিন্তু শ্রবণের বিচারে যুক্ত। কান তাকে “ভপুর’ হিসেবেই গ্রহণ করেছে। এবং ছন্দবিচারে চোখ নয়, কানই যে হাকিম, তা কে না জানে!
অক্ষরের চাইতে ধ্বনি বড়ো। অক্ষর তো আর-কিছুই নয়, ধ্বনিরই একটা দৃশ্যরূপ মাত্র। আসলে যা ধর্তব্য, তা হচ্ছে ধ্বনি। তাই, চোখের নয়, কানের রায়ই শিরোধার্য। আর তাই, অক্ষরবৃত্তের লাইনে চার অক্ষরের শব্দ ‘কলকাতাকে অক্লেশে তিন-মাত্রা হিসেবে চালানো যায় (কেন-না। কান তাকে কল্কতা” বলে জানে), পাঁচ-অক্ষরের শব্দ “খিদিরপুর’কে চালানো যায় চার-মাত্রা হিসেবে (কেন-না কনের কাছে সে খিদিপুর), ছ-অক্ষরের শব্দ ‘কারমাইকেল’কে তারিয়ে দেওয়া যায় পাঁচ-মাত্রার মাশুল দিয়ে (কেন-না কর্ণে তিনি কাৰ্মাইকেল)। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের এই একটা মস্ত সুবিধে। যেখানে সম্ভব, শব্দকে সেখানে অক্ষরের তুলনায় কম-মাত্রার মাশুল দিয়ে তারানো যায়, ছন্দের ভারসাম্য তাতে নষ্ট হয় না। আবার তার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :
চারজন হাড়গিলে-ছোকরা ঘুরবার বাতিকে
কাতরাতে কাতরাতে চলল হাতিরাসের দিকে।
লক্ষ করে দেখুন, এই লাইন দুটির প্রত্যেকটিতেই অক্ষরের সংখ্যা আঠারো। কিন্ত তা সত্ত্বেও এরা চোদ্দো মাত্রার লাইন হিসেবে চলতে পারে। তার কারণ, চক্ষু এদের যে-চেহারাই দেখুক, কানের কাছে সংকুচিত হয়ে গিয়ে এরা এই রকমের চেহারা নেয় :
চার্জন হার্গিলে ছোক্ৰা ঘুর্বার বাতিকে
কাত্ৰাতে কাত্ৰাতে চল্লি হাত্ৰাসের দিকে।
আবার বলি, ছন্দের ব্যাপারে অক্ষর-বস্তুটা কিছু নয়, সে ধ্বনির-প্রতীক মাত্র, এবং ধ্বনিটাই হচ্ছে একমাত্র ধর্তব্য বিষয়। পরে তার আরও অজস্র প্রমাণ মিলবে।
বুদ্ধিমান পড়ুয়া আশা করি ইতিমধ্যেই একটা জরুরি কথা বুঝে নিয়েছেন। সেটা এই যে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দ সংকোচনকে প্রশ্রয় দেয়, আর তাই হসন্ত অক্ষরমাত্রেই সেখানে পরবতী অক্ষরের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে তার আত্মস্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দিতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বিশেষত, যুক্ত হবার বিধি যেখানে আছেই, সেখানে— দৃশ্যত আলাদা থাকলেও— শ্রবণের বিচারে যুক্ত হতে তাদের কিছুমাত্র আটকায় না। ল’য়ে ক’য়ে মিলন প্রথাসম্মত বলেই ‘কলকাতা’ আমাদের শ্রবণে ‘কল্কাতা’ হয়, ‘ত’য়ে ‘ত’য়ে মিলন রীতিসিদ্ধ বলেই ‘পাততাড়ি’ গুটিয়ে গিয়ে হয় ‘পাত্তাড়ি’।
কিন্তু মিলন যেখানে রীতিসিদ্ধ নয়, শ্রবণ কি সেখানেও অসবর্ণ বিবাহে অনুমোদন দেয়? তা-ও দেয়। এবং আমি যতদূর জানি, রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম, শ্রবণের অনুমোদন নিয়ে, সেই অসবর্ণ মিলন ঘটাতে সাহসী হয়েছিলেন। ‘আকবর বাদশার সঙ্গে হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই”- “বাঁশি” কবিতার এই লাইনটির সঙ্গে সকলেই পরিচিত। ছন্দ অক্ষরবৃত্ত। তার প্রশ্রয়ে ‘আকবর’ হয়েছে তিন-মাত্রা; বাদশার শব্দটিও তা-ই। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, কয়ে ‘ব’য়ে মিলন রীতিবিরুদ্ধ নয় বটে, কিন্তু সেই ‘ব’-ফলায় ইংরেজি ‘বি’-অক্ষরের ধ্বনি আসে না (দৃষ্টান্ত; পকৃ, নিকৃণ), এক্ষেত্রে কিন্তু সেই ধ্বনিকে সম্পূর্ণ বঁচিয়েই কবি তাকে ‘কায়ের সঙ্গে জুড়েছেন। ‘বাদশা’র ব্যাপারটাও সমান চমকপ্ৰদ। ‘দ’য়ে শ’য়ে যুক্ত হবার রীতি নেই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তবু অসম সাহসে তাদের মিলিয়ে দিয়েছেন।*
একালের কবিতায় অবশ্য এমন অসবর্ণ মিলন আকছার ঘটতে দেখি। কিন্তু ভুলে না। যাই যে, রবীন্দ্রনাথই এই দুঃসাহসিক মিলনের প্রথম পুরোহিত। অক্ষরবৃত্ত সম্পর্কে আমাদের ক্লাসে এযাবৎ যেসব কথাবার্তা হল, তার থেকে ছেকে নিয়ে মোদা কথাটা তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে :
১) ৪ কিংবা তার গুণিতকের সঙ্গে ২ যোগ করলে যে-সংখ্যাটা পাওয়া যায়, সেই সংখ্যার মাত্রা দিয়েই তৈরি করা যায় অক্ষরবৃত্ত কবিতার লাইন।
২) এ-ছন্দ শব্দের সংকোচনকে প্রশ্ৰয় দেয়; তাই শব্দের ভিতরকার হসন্ত অক্ষর এ-ছন্দে পরবতী অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত হতে চায়। দৃশ্যত যেখানে তারা যুক্ত হয় না, সেখানেও তারা শ্রবণে যুক্ত হয়; ফলে দৃশ্যত তারা পৃথক থাকে বটে, কিন্তু শ্রবণে তারা মিলিত হয়ে দুয়ে মিলে একটিমাত্র মাত্রার মর্যাদা পায়।
৩) দুটি অক্ষরের মিলন যেখানে রীতিসিদ্ধ, সেখানে তো শ্রবণের অনুমোদন নিয়ে মিলিত হয়ই (খিদিরপুর = খিদিপুর = ৪ মাত্রা),- মিলন যেখানে রীতিসিদ্ধ নয়, সেখানেও অনেকসময়ে শ্রবণের ঔদার্যে তাদের অসবৰ্ণ বিবাহ ঘটে, এবং অক্ষরবৃত্ত ছন্দ তাতেও বোজার হয় না (বাদশা = ২ মাত্রা)।
অক্ষরবৃত্তে এই অসবর্ণ মিলনের সুন্দর একটি দৃষ্টান্ত আমরা রবীন্দ্রনাথের ‘বাঁশি’ কবিতা থেকে তুলে দিয়েছি। এবারে দেখা যাক, আমরা নিজেরাও এইভাবে অক্ষরে-অক্ষরে অসবৰ্ণ বিবাহ ঘটাতে পারি, কি না।
বাজনা বাজে পূজার প্রাঙ্গণে;
ফোটেনি সজনের কুঁড়িগুলি।
খাজনার আতঙ্ক জাগে মনে,
শস্য খেয়ে গিয়েছে বুলবুলি।
এ-ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দেরই কবিতা। এর ফি-লাইনে অক্ষরের সংখ্যা এগারো বটে, কিন্তু মাত্রার সংখ্যা দশ। তার কারণ আর-কিছুই নয়, ফি-লাইনে এমন এক-একটা শব্দ আছে, ভিতরে হসন্ত অক্ষর থাকায় শ্রবণে যা সংকুচিত হয়ে যায়। প্রথম লাইনে সেই শব্দটি হচ্ছে বাজনা” (শ্রবণে গুটিয়ে গিয়ে সে দু-মাত্রার মর্যাদা পায়), দ্বিতীয় লাইনে সেই শব্দটি হচ্ছে “সজনের” (শ্রবণে গুটিয়ে গিয়ে সে তিন-মাত্রায় দাঁড়াচ্ছে), তৃতীয় লাইনে সেই শব্দটি হচ্ছে ‘খাজনার’ (শ্রবণে সে-ও গুটিয়ে গিয়ে হচ্ছে তিন-মাত্রার শব্দ), আর চতুর্থ লাইনের সেই শব্দটি হচ্ছে “বুলবুলি” (কানের কাছে যার সংকুচিত শরীরের মূল্য মাত্র তিন-মাত্রা)। প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরবর্তী অক্ষরের সঙ্গে শব্দের মধ্যবর্তী হসন্ত অক্ষরের মিলন। এখানে অসবর্ণ। (প্রথম তিনটি ক্ষেত্রে জীয়ে নিয়ে মিলন ঘটেছে, যা রীতিবিরুদ্ধ। চতুর্থ ক্ষেত্রে মিলন ঘটেছে ল’য়ে আর ইংরেজি ‘বি’ অক্ষরের ধ্বনিসম্পন্ন ব’য়ে; তা-ও রীতিসিদ্ধ নয়। চোখের বিচারে তারা অবশ্য আলাদাই রইল, শুধু কানের বিচারেই তারা মিলিত)
এখন একটা মজার কথা বলি। অক্ষরের এই মিলন-লীলা যে নেহাতই ঘরোয়া, অর্থাৎ একই শব্দের গণ্ডির মধ্যে যে এই মিলন চলে, তা কিন্তু নয়। এতক্ষণ অবশ্য শুধু ঘরোয়া মিলনেরই দৃষ্টান্ত দিয়েছি। এইবার বলি, এক বাড়ির মেয়ে যেমন অন্য বাড়ির ছেলের প্রেমে পড়ে, তেমনি এক-শব্দের অক্ষর অনেকসময়ে আর-এক শব্দের অক্ষরের সঙ্গে হাত মেলাতে চায়। সেসব ক্ষেত্রে দেখা যায়, শব্দের প্ৰান্তবতী হসন্ত অক্ষরটি পরবতী শব্দের আদ্যক্ষরের সঙ্গে মিলিত হতে চাইছে। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :
কালকা মেলে টিকিট কেটে সে
কাল গিয়েছে পাহাড়ের দেশে
এর মধ্যে, অক্ষর-সংখ্যা যা-ই হোক, ‘কালকা মেলে’ শব্দ দুটির মোট মাত্ৰা-সংখ্যা ৪; ‘কাল গিয়েছে’র মাত্ৰা-সংখ্যাও তা-ই। কানের কাছে এদের প্রথমটির চেহারা ‘কাল্কা মেলে’; দ্বিতীয়বার চেহারা ‘কাল্গিয়েছে’। অক্ষরে-অক্ষরে মিলন ঘটেছে দুটি ক্ষেত্রেই। কিন্ত প্রথম ক্ষেত্রে সে-মিলন ঘরোয়া (“কালকা’ শব্দটার মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ)। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মিলন ঘটেছে এক শব্দের (কলা) শেষ অক্ষরের (যা কিনা হসন্ত) সঙ্গে তার পরবতী শব্দের (গিয়েছে) প্রথম অক্ষরের।
এইখানে একটা কথা বলে রাখি। অক্ষরে-অক্ষরে মিলন ঘটিয়ে, যুক্তাক্ষরের মায়া সৃষ্টি করে, মাত্রা কমাতে মজা লাগে, বলাই বাহুল্য। কিন্তু মজা লাগে বলেই যে প্রতি পদে এইভাবে মিলন ঘটাতে হবে, তা কিন্তু ঠিক নয়। এসব সেয়ানা কৌশল বারবার খাটালে এর চমকটাই আর থাকে না, পাঠকও বিরক্ত বোধ করেন। আর তা ছাড়া, কবিতার মধ্যে এই ধরনের মিলনের বাড়াবাড়ি ঘটলে ছন্দ-অনুসরণেও তাঁর অসুবিধে ঘটে। লক্ষ রাখতে হবে, কবিতার ছন্দের মধ্যে পাঠক যেন বেশ স্বচ্ছন্দে ঢুকতে পারেন; তারপর ভিতরে ঢুকে যখন কিনা বেশ অনায়াসে তিনি চলাফেরা করে বেড়াচ্ছেন, তখন বরং এই ধরনের এক-আধটা চমক লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে, সেটা তার ভালোই লাগবে।
আর-একটা কথা এই যে, লাইনের যে-কোনও জায়গায় কিন্তু এইভাবে অক্ষরেঅক্ষরে মিলন ঘটানো সম্ভবও নয়। অক্ষরবৃত্তের যে একটা চার-মাত্রার ছোটো চাল আছে, সেহিচালের পর্বের মধ্যেই মিলনটাকে ঘটিয়ে দেওয়া ভালো। মিলন ঘটাতে গিয়ে যদি পর্বোেব বেড়া ডিঙিয়ে যাই, তাতে বিপদ ঘটতে পারে। ঘটেও।
এবারে একটা জরুরি কথা বলি। কবিতা লিখতে গিয়ে লক্ষ রাখতে হবে, শব্দের উচ্চারণ আর ছন্দের চাল, এ দুয়ের মধ্যে যেন ঠিকঠাক সমন্বয় ঘটে। অর্থাৎ ছন্দের চাল ঠিক রেখে কবিতা পড়তে গিয়ে যেন দেখতে না পাই যে, ছন্দের খাতিরে শব্দের শরীরকে এমন-এমন জায়গায় ভাঙতে হচ্ছে, যেখানে তাদের ভাঙা যায় না। আবার শব্দের সঠিক উচ্চারণের খাতিরে ছন্দের চাল যেন বেঠিক জায়গায় না। ভাঙে। বেঠিক জায়গায় চাল ভাঙলে ছন্দের নাভিশ্বাস উঠবে। এই বিভ্ৰাট যদি এড়াতে হয় তাহলে ছন্দের চাল আর শব্দের উচ্চারণ, এই দুইয়ের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার একটা সুন্দর সম্পর্ক গড়ে তোলা চাই। উপমা দিয়ে বলি, ছন্দের চাল আর শব্দ যেন একই-গাড়িতে-জুতে-দেওয়া দুই ঘোড়ার মতন। লক্ষ রাখতে হবে, সেই ঘোড়া দুটি যেন পরস্পরের বিপরীত দিকে ছুটতে না চায়। গাড়ি তাহলে এক-পাও এগোবে না। গাড়ি যাতে ঠিকমতো এগোয়, তারই জন্যে চাই ঘোড়া দুটির মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক।
এই সম্পর্ক গড়ে তুলতে না পারলে, অঙ্কের নিয়মে সবকিছু ঠিকঠাক থাকা সত্ত্বেও, বিপদ কীভাবে অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়, একটু বুঝিয়ে বললেই সেটা পরিষ্কার হয়ে যাবে।
ধরা যাক, আমরা চোদ্দো-মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে দু-লাইন কবিতা লিখতে চাই। তার বিষয়টা এই যে, উঁচুনিচু বৃক্ষ পথে হেঁটে-হেঁটে যাত্রীদের জীবন কেটে গেল। তা কথাটাকে যদি এইভাবে বলি :
অসমতল অমসৃণ পন্থায় হেঁটে
যাত্রীদের গিয়াছে সারা জীবন কেটে
তাহলে কি ঠিক হবে?
না, হবে না। অঙ্কের হিসেবে অবশ্য সবকিছু এখানে ঠিকঠাক আছে, ফিলাইনে চোদ্দো মাত্রার বরাদ্দ চাপাতে কোনও ত্রুটি ঘটেনি; তবু কান বলছে, ঠিক হল না। তার কারণ ঘোড়া দুটো এখানে দু-দিকে ছুটি লাগিয়েছে; ছন্দের চাল আর শব্দের উচ্চারণে বিরোধ ঘটছে পদে-পদে। ছন্দের চাল ঠিক রেখে এই লাইন দুটিকে যদি পড়তে যাই, তো এইভাবে পড়তে হয় :
অসমত/ল অমসৃ/ণ পন্থায়/হেঁটে
যাত্রীদের/গিয়েছে সা/রা জীবন/কেটে
অর্থাৎ, শব্দগুলিকে বেজায়গায় ভাঙতে হয়। কিন্তু শব্দকে তো আমরা তেমনভাবে ভাঙতে পারিনে। বলা বাহুল্য, ছন্দের খাতিরে শব্দকে অনেকসময়ে ভেঙে পড়তে হয়, কিন্তু সেই ভাঙারও একটা নিয়ম আছে, খেয়ালখুশিমতো যে-কোনও জায়গায় তাকে ভাঙা চলে না। শব্দ যদি ভাঙতেই হয়, তো নিয়ম মেনে এমনভাবে ভাঙতে হবে, যাতে কানের সমর্থন পাওয়া যায়। সুতরাং, হয় শব্দকে আদৌ না-ভেঙে লাইন দুটিকে আমরা এইভাবে লিখব :
অমসৃণ/অতিরুক্ষ/পথে-পথে/হেঁটে
যাত্রীদের/জীবনের/দিন গেল/কেটে
আর নয়তো ভাঙতে হলেও, কনের সমর্থন নিয়ে, এইরকমভাবে শব্দ ভাঙব :
বন্ধুর দা/রুণ রুক্ষ/পথে-পথে/হেঁটে
যাত্রী-জীব/নের দিন/রাত্রি গেল/কেটে
এই রকমে যদি শব্দ ভাঙি, তাহলে অক্ষরবৃত্তের ছোটো চালে (অর্থাৎ চার-মাত্রার চালে) যদি-বা ভাঙােটা চোখে পড়ে, বড়ো চালে (অর্থাৎ ৮+৬। মাত্রার চালে) সেটা আদৌ ধরা পড়ে না। ব্যাপারটা তখন এইরকম দাঁড়ায় :
বন্ধুর দারুণ বুক্ষ/পথে পথে হেঁটে
যাত্রী-জীবনের দিন/রাত্রি গেল কেটে
তাহলেই দেখা যাচ্ছে যে, ছন্দবিভ্ৰাট এড়াতে হলে লাইনে-লাইনে মাত্রার সংখ্যা ঠিক রাখাটাই যথেষ্ট নয়, শব্দগুলিকে সাজিয়ে বসাবার ব্যাপারেও নিয়ম রক্ষা করা চাই। নিয়মের সারকথাটা কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তই বলে গিয়েছেন। তার পরামর্শ: “বিজোড়ে বিজোড় গাঁথি, জোড়ে গাঁথি জোড়।” অর্থাৎ কিনা বিজোড়-শব্দের পিঠে বিজোড়-শব্দ বসাতে হবে, জোড়-শব্দের পিঠে। জোড়। শব্দের ব্যাপারে। জোড়-বিজোড় কাকে বলে, সেটা বুঝতে কারও অসুবিধে হবার কথা নয়। যে-শব্দের অক্ষরসংখ্যা বিজোড়, সেটা বিজোড়-শব্দ। যে-শব্দের অক্ষরসংখ্যা জোড়, সেটা জোড়-শব্দ। মোদ্দা কথাটা তাহলে এই দাঁড়াচ্ছে যে, দুই কিংবা চার অক্ষরের শব্দের পিঠে জোড়-শব্দ বসাতে হবে; এক কিংবা তিন অক্ষরের শব্দের পিঠে বিজোড়-শব্দ। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের চাল ঠিক রাখবার ব্যাপারে। এইটেই হচ্ছে সবচাইতে নিরাপদ নিয়ম।
*
এখন আমাদের আলোচনাকে একটু পিছিয়ে নিতে চাই। তার কারণ, অক্ষরে-অক্ষরে মিল ঘটিয়ে যুক্তাক্ষরের মায়া সৃষ্টি করে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে মাত্রা চুরি করা সম্পর্কে এর আগে যেসব কথা বলেছি, একটা জরুরি কথাই তাতে বাদ পড়ে। গিয়েছিল। আমার মাসতুতো ভাইয়ের সেই পদ্য-লিখিয়ে কনিষ্ঠ পুত্র সেটা মনে করিয়ে দিল। বুড়ো হয়েছি, সব কথা সর্বদা মনে থাকে না, চিন্তার শৃঙ্খলা নষ্ট হয়েছে, পরের কথাটা অনেকসময়ে আগেই বলে বসি, আগের কথার খেই হারিয়ে যায়, এগিয়ে গিয়েও মাঝে-মাঝে তাই পিছনে তাকাবার প্রয়োজন ঘটে। তাকিয়ে বুঝতে পারছি, জরুরি সেই কথাটা এবারে চুকিয়ে দেওয়া দরকার, নয়তো পরে আবার হয়তো ভুলে যাব।
কথাটা সংক্ষেপে এই :
অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ‘কলকাতা’ যে সহজেই ‘কল্কাতা’ (অর্থাৎ ৩ মাত্রা) হয়ে যায়, তা আমরা দেখেছি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, অক্ষরবৃত্তে কবিতা লিখতে গিয়ে ‘কলকাতা’কে আমরা ৪-মাত্রার শব্দ হিসেবে ব্যবহার করতে পারব না। আসলে, শব্দটাকে আমরা কীভাবে উচ্চারণ করব, তারই উপর নির্ভর করছে সে ক-মাত্রার মর্যাদা পাবে। গোটানো উচ্চারণে সে ৩-মাত্রার শব্দ বটে, কিন্তু ছড়ানো উচ্চারণে সহজেই সে আবার চার মাত্ৰা দাবি করতে পারে। নীচের লাইন দুটি লক্ষ করুন :
উচ্চারণভেবে হয় মাত্রাভেদ ভ্রাতা,
না হলে কলকাতা কেন হবে কলকাতা?
বুঝতেই পারছেন, দ্বিতীয় লাইনে ‘কলকাতা’ শব্দটিকে দু-বারে দু-রকমে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম বারে সে গোটানো উচ্চারণে ৩-মাত্রা (কঙ্কাতা); দ্বিতীয় বারে সে ছড়ানো উচ্চারণে ৪-মাত্রা।
অক্ষরবৃত্ত ছন্দে, এইভাবে, উচ্চারণের তারতম্য অনুযায়ী, “খিদিরপুরীকে ৪মাত্ৰাও করা যায়, ৫-মাত্ৰাও করা যায়। ‘হ’ল’ক’কে ২-মাত্ৰাও করা যায়, ৩-মাত্ৰাও করা যায়। শরবতীকে করা যায়। কখনও ৩-মাত্রা কখনও ৪-মাত্রা। কয়েকটি লাইন দেখুন :
শহরের দক্ষিণেতে ‘খিদিরপুরে’তে
গিয়ে যদি খিদে পায়, কিছু হবে খেতে।
যদি দ্যাখো ‘খিদিরপুরে’ খাদ্যের দোকান
বন্ধ, তবে খেয়ে নিয়ো এক খিলি পান।
দ্বিপ্রহরে বাতাসের তপ্ত ‘হালকা’য়।
রাজপথে যদি বাছা মাথা ঘুরে যায়,
তদুপরি পেটে যদি ক্ষুধার ‘হলকা’-ও
চলে, তবে পান ছাড়া অন্য কিছু খাও।
কলেরার ভয় যদি না-ই থাকে প্রাণে,
‘শরবত’ খেতে পারো পানের দোকানে।
যদি নাড়ি ছাড়ে, তবু মনে রেখো প্রিয়,
ঘোলের শরবত অতি উত্তম পানীয়।
বলাই বহুল্য, কবিতায় যা-ই লিখি না কেন, কলেরার সুই যদি না-নিয়ে থাকেন, তবে আর যা-ই করুন, যত্রতত্র শরবত খাবেন না। কিন্তু সেটা কোনও কথা নয়। একটু লক্ষ করলেই বুঝতে পারবেন, খিদিরপুরীকে এখানে প্রথম বারে ৫-মাত্রা ও দ্বিতীয় বারে ৪-মাত্রা, ‘হালকা’কে এখানে প্রথম বারে ৩-মাত্রা ও দ্বিতীয় বারে ২-মাত্রা, এবং শরবতকে এখানে প্রথমবারে ৪-মাত্রা ও দ্বিতীয় বারে ৩-মাত্রার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের শব্দ আসলে গোটানো ও ছড়ানো দ্বিবিধ উচ্চারণের শাসনই মেনে চলে, এবং উচ্চারণ অনুযায়ী এদের মাত্ৰাসংখ্যারও তারতম্য হয়।
তবে একটা কথা। এখানে ব্যবহার করেছি বটে, কিন্তু এই ধরনের শব্দকে একই কবিতার দুই সন্থানে দু-রকম মাত্রার মর্যাদা দিয়ে ব্যবহার করাটা ঠিক নয়। কবিতার মধ্যে এসব শব্দকে একবার যদি গোটানো উচ্চারণের শাসনে আনি, তো অন্তত সেই কবিতায় তাদের আর ছড়ানো উচ্চারণের স্বাধীনতা না দেওয়াই ভালো। দিলে তাতে মহাকাব্য অশুদ্ধ না হোক, পাঠককে অসুবিধেয় ফেলা হয়। ডাবল স্ট্যানডারড জিনিসটা কোনও ক্ষেত্রেই ভালো নয়। কবিতাতেও তাকে প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত।
সুতরাং অক্ষরবৃত্তে কবিতা লিখতে বসে আগেভাগেই স্থির করে নিন, যেসব শব্দ দ্বিবিধ উচ্চারণকেই মান্য করে, ঠিক কীবিধ উচ্চারণে আপনি তাদের বাধবেন। একবার যদি তাদের কাউকে গোটানো উচ্চারণে শক্ত করে বাঁধেন, তো অন্তত সেই কবিতায় অন্যত্র তার বাঁধনে আর ঢ়িল দেওয়া ঠিক নয়। কলকাতা’ আপনার কবিতায় যদি একবার গোটানো উচ্চারণে ৩-মাত্রার মূল্য পায়, তবে সেই কবিতাতেই পরে আর তাকে (কিংবা সেই রকমের অন্য কোনও শব্দকে) ছড়ানো উচ্চারণে বেশিমাত্রার মর্যাদা দেওয়া অনুচিত হবে। উপমা দিয়ে বলতে পারি, ব্যাপারটা হচ্ছে গান গাইবার আগে ‘স্কেল” ঠিক করে নেবার মতো। গান গাইতে-গাইতে মাঝপথে যেমন স্কেল পালটানো চলে না, কবিতা লিখতে-লিখতে তেমনি মাঝপথে উচ্চারণের বাঁধুনি পালটানো চলে না। কোন রকমের বাঁধুনি আপনার মনঃপূত, সেটা আগেই ঠিক করে নিন; মাঝপথে রীতিবদল না করাই ভালো।
সকলে এ-ব্যাপারে একমত নন, আমি জানি। সবাইকে আমার দলে টানতে পারব, এমন আশাও আমি করিনে। তবু আমি, শ্ৰীকবিকঙ্কণ সরখেল, যে-রীতিকে উচিত বলে মানি, অকপটে তা নিবেদন করলুম। অক্ষরবৃত্ত সম্পর্কে আমাদের আলোচনা এখনকার মতো এইখানেই শেষ হল।
আপনারা হয়তো ভাবছেন, এত যে কথা হল, পয়ারের প্রসঙ্গ এখনও উঠল না। কেন। ওঠেনি, তার কারণ, পয়ার আসলে আলাদা কোনও ছন্দ নয়, ছন্দের বাঁধুনিরই সে একটা রকমফের মাত্র। মূল তিনটি ছন্দের মোটামুটি পরিচয় আগে বিবৃত করি, তারপর পয়ারের প্রসঙ্গ ঢোকা যাবে।
—————-
* ‘পরিশিষ্ট’-অংশে জিজ্ঞাসু পড়ুয়ার চিঠি দেখুন।
০৫. মাত্রাবৃত্ত বা কলাবৃত্ত বা ধ্বনিপ্রধান ছন্দ
অক্ষরবৃত্তের পরিচয় মোটামুটি মিলেছে, এবার শুরু হবে মাত্রাবৃত্তের কথা। মাত্রাবৃত্ত নামটাও শ্ৰীপ্ৰবোধচন্দ্র সেনের দেওয়া। রবীন্দ্রনাথ একে সংস্কৃত-ভাঙা ছন্দ বলতেন। শ্ৰীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায়। সেক্ষেত্রে এর নাম দিয়েছেন ধ্বনিপ্রধান ছন্দ। যেমন অক্ষরবৃত্ত তেমনি মাত্রাবৃত্ত নামটিকেও প্রবোধচন্দ্র পরে বর্জন করেন; এবং এর নতুন নাম দেন কলাবৃত্ত। তাঁর আলোচনায় এখন এই নতুন নামটিই চালু। আমাদের আলোচনায় অবশ্য মাত্রাবৃত্ত নামটিই ব্যবহৃত হবে।
এবারে আসল কথায় আসি। গোড়ার দিকে যখন তিন-ছন্দের পার্থক্য একবার দেখিয়ে দিয়েছিলুম, তখন মাত্রাবৃত্তের দৃষ্টান্তও এক-আধটা দেওয়া হয়েছে। বলাই বাহুল্য, আলাদা আলাদা ছন্দের দৃষ্টান্ত যদি পাশাপাশি তুলে ধরা যায়, তাদের চরিত্রের পার্থক্য তাহলে সহজে ধরা পড়ে; বুঝতে পারা যায়, একটার সঙ্গে আর-একটার অমিল কোনখানে, চালচলনে ঠিক কোথায় তারা আলাদা।
দৃষ্টান্ত দিয়ে-দিয়ে পার্থক্য ধরিয়ে দেবার সেই কাজটা এবার আর-একটু বিশদভাবে করা যেতে পারে। তার কারণ অক্ষরবৃত্তকে আপনারা চিনে গিয়েছেন। এখন তারই পাশে যদি মাত্রাবৃত্তকে তুলে ধরি, তাদের পার্থক্য তাহলে চট করে ধরা পড়বে; বুঝতে পারা যাবে, কোন ছন্দ কীভাবে হাঁটছে, এবং দুজনে দুভাবে হাঁটছেই বা কেন।
ধরা যাক, সময়টা কীর্তিক মাস, এবং বাতাসের দাঁত খানিকটা ধারালো হয়ে উঠেছে, এই খবরটাকে আমরা পদ্যে পরিবেশন করতে চাই। সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি :
কার্তিক-নিশীথে আজ পাচ্ছি বেশ টের
দন্তের আভাসটুকু প্রথম-শীতের।
তা এই লাইন দুটি যে কোন ছন্দে লেখা হয়েছে, তা বুঝবার জন্যে এখন আর আপনাদের মাস্টারমশাইয়ের সাহায্য নেবার দরকার করে না। একবারমাত্র শুনেই এখন আপনারা বলে দিতে পারেন যে, এটা অক্ষরবৃত্ত। এ-ছন্দের চাল আপনারা চিনে গেছেন। কান যদি খোলা থাকে, তাহলে চোখ বুজেও এখন একে আপনারা শনাক্ত করতে পারেন। তাই না? এবারে আসুন, প্রথম-শীতের এই সংবাদটাকে অন্য ছন্দে পরিবেশন করা যাক। লেখা যাক :
এবারে এসেছে কার্তিক; তার
উত্তুরে বাতাসের
বরফে-ডোবানো দন্তের ধার
রাত্তিরে পাই টের।
বুঝতেই পারছেন, যে, সংবাদটার মধ্যে একটু অতিরঞ্জন আছে। কেন-না কার্তিক মাসে শীত কিছুটা পড়ে ঠিকই, কিন্তু বাতাসের দাঁত তাই বলে এমন-কিছু ধারালো হয়ে ওঠে না। অন্তত তখনই এমন মনে হয় না যে, সে-দাঁত বরফে-ডোবানো। তা সে যা-ই হোক, সংবাদ নিয়ে আমরা এখানে মাথা ঘামাচ্ছিনে, আমরা শুধু ছন্দের পার্থক্যটা দেখে নিতে চাই, এবং এখানে যে-ছন্দে এই খবরটাকে আমরা বেঁধেছি, তা যে অক্ষরবৃত্ত নয়, চালের পার্থক্য থেকেই তা আমরা বুঝতে পারছি।
এ হল মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। অক্ষরবৃত্তের সঙ্গে একে একবার মিলিয়ে নিন। মেলাতে গেলেই অমিলটা বেশ স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়বে।
আরও কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। পাশাপাশি এই দুই ছন্দের চেহারা দেখতে দেখতে এদের অমিলটা যখন একেবারে স্পষ্ট হয়ে যাবে, তখনই শুরু হবে মাত্রাবৃত্তের চরিত্রবিচার। আগেই যদি চরিত্রবিচার করতে বসি, ব্যাপারটা তাহলে অত সহজে পরিষ্কার হবে না। কার চরিত্র কী রকমের সেটা বস্তৃতা দিয়ে বোঝানো শাস্তু; দৃষ্টান্তের সাহায্য নিলে সে-কাজ অনেক সহজে সম্পন্ন হয়। যার পিঠে কখনও কিল পড়েনি, তাকে যদি বলি, “কিল বলিতে বদ্ধমুষ্টির সাহায্যে প্রদত্ত এক প্রকারের আঘাত বুঝায়”—তবে আর তার কতটুকুই-বা সে বুঝবে? তার চাইতে বরং গুম করে তার পিঠের উপরে একটা কিল বসিয়ে দেওয়া ভালো।
সুতরাং আসুন, মাত্রাবৃত্তের বৈশিষ্ট্য কী, হাতে-কলমে সেটা বুঝে নিই। অর্থাৎ, অক্ষরবৃত্তের পাশাপাশি আরও কয়েক বার তার চেহারাটা বেশ উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করি, এবং বুঝবার চেষ্টা করি, অক্ষরবৃত্তের সঙ্গে তার তফাতটা ঠিক কোথায়।
ধরা যাক, আমরা রেলগাড়ি নিয়ে দু-লাইন পদ্য বানাব। গর্জন করে ট্রেন ছুটছে, এবং সেই গর্জন শুনে মাঠের গোরু দিগন্তের দিকে দৌড় লাগাচ্ছে, এই হবে তার বিষয়বস্তু।
লাইন দুটিকে প্রথমে আমরা অক্ষরবৃত্তে লিখব। তা এইভাবে তাকে লেখা যেতে পারে :
গর্জন কম্পিত বিশ্ব, ট্রেন ছুটে যায়;
আতঙ্কে গোরুর দল দিগন্তে পালায়।
এবারে এই কথাগুলিকে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে বেঁধে ফেলা যাক। এইভাবে বাঁধা যেতে পারে :
গর্জন কাঁপে মাটি, ট্রেন ছুটে যায়।
আতঙ্কে গোরুগুলি দিগন্তে ধায়।
কানের কাছে তফাতটা আশা করি ধরা পড়েছে। এবার আসুন, আর-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। এবারে কী নিয়ে পদ্য লিখব? প্রেম নিয়ে? ভালো ভালো, পদ্য রচনার পক্ষে প্ৰেম অতি চমৎকার বিষয়বস্তু। তা ধরা যাক, প্রেমিক তার প্রেমিককে বলছে যে, সে (অর্থাৎ প্রেমিক) যদি তাকে (অর্থাৎ প্রেমিকাকে) পাশে পায়, তাহলে দৈত্যের সঙ্গেও সে (অর্থাৎ প্রেমিক) লড়তে রাজি। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে এই কথাগুলিকে এইভাবে বাঁধা যায় :
তুমি যদি সারাক্ষণ পার্শ্বে থাকো নারী,
দৈত্যকেও তবে আমি যুদ্ধ দিতে পারি।
অনেকে হয়তো বলবেন যে, প্রেমিকের উক্তিটা এক্ষেত্রে একেবারেই যাত্রাপ্যাটার্নের হয়ে গেল। তা হোক, এ তো আর একালের আটাশ-ইঞি-বুকের-ছাতি লিন্কপিকে প্রেমিক নয় যে, মিনমিনে গলায় কথা বলবে। আর কেঁচার খুঁটে চোখের জল মুছতে-মুছতে ঘন-ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবে। এ হচ্ছে সেকালের বীরপুরুষ প্রেমিক। সেকালে প্রেমিকেরা বনবান করে তলোয়ার ঘোরাত এবং ঘ্যাচাং করে। দৈত্যদানের মুণ্ডু কেটে ফেলত। সুতরাং তাদের উক্তিতে যদি একটু বীরত্বের বড়াই থাকে, তবে তা নিয়ে এত আপত্তির কী আছে! আর তা ছাড়া উক্তি নিয়ে আমরা এখানে মাথা ঘামাচ্ছিনে, আমরা ছন্দের পার্থক্য বুঝতে চাই। সুতরাং পার্থক্যটাকে বুঝে নেবার জন্য, আর কথা না বাড়িয়ে, এই উক্তিটিকে এবারে আমরা মাত্রাবৃত্তে বাঁধব। এইভাবে বাঁধা যাক :
তোমাকে যদি পার্শ্বে পাই,
তাহলে আমি, নারী
দৈত্যকেও অকুতোভয়ে
যুদ্ধ দিতে পারি।
পার্থক্যটা বুঝতে পারছেন? নিশ্চয়ই পারছেন। তবু আসুন, আরও একটা দৃষ্টান্তের সাহায্য নেওয়া যাক।
এবারে আমরা কী নিয়ে লিখব? প্রেম নিয়ে তো লিখলুম, এবারে বিরহ নিয়ে লেখা যেতে পারে। অক্ষরবৃত্তে আমাদের বিরহী নায়কের উক্তিটা এই রকমের চেহারা নিচ্ছে :
যে নেই সম্মুখে, কানে কণ্ঠ তার বাজে;
দিন চলে যায়, তবু রাত্রি যায় না যে।
আবার মাত্রাবৃত্তে এই একই কথাকে আমরা এইরকমে বাঁধতে পারি। :
সম্মুখে নেই, তবু কানে কানে
কণ্ঠ তাহারি বাজে,
দিন চলে যায়, দিবা অবসানে
নিশীথিনী যায় না যে।
আর নয়। অনেক দৃষ্টান্ত দিয়েছি। অক্ষরবৃত্তের দৃষ্টান্তগুলির সঙ্গে মাত্রাবৃত্তের দৃষ্টান্তগুলিকে এবারে উত্তমরূপে আর-একবার মিলিয়ে নিন। তাদের পার্থক্য বুঝতে তাহলে আর এতটুকু অসুবিধে হবে না।
কথা এই যে, পার্থক্য যেমন অক্ষরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তের মধ্যে আছে, তেমনি আবার মাত্রাবৃত্তের আপনি এলাকাতেও আছে। অর্থাৎ এক-ধরনের মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে অন্য-ধরনের মাত্রাবৃত্তের আছে। মাত্রাবৃত্তের ধরন মাত্র একটি নয়, অনেক। পার্থক্য তাদের নিজেদের মধ্যেও আছে বটে, কিন্তু সেই ঘরোয়া পার্থক্যের প্রকৃতিও পৃথক।
সে কথা পরে। মাত্রাবৃত্তের মধ্যেকার ঘরোয়া পার্থক্যের কথা পরে বোঝা যাবে। তার আগে অক্ষরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তের মৌলিক পার্থক্যটা বুঝে নেওয়া চাই।
অক্ষরবৃত্তের মোটামুটি নিয়মটা আশা করি ইতিমধ্যে আপনারা ভুলে যাননি। ‘মোটামুটি” কথাটা ব্যবহার করলুম। এইজন্যে যে, নিয়মের ব্যতিক্রমও নেহাত কম নয়। কিছু কিছু ব্যতিক্রমের হদিসও আমরা পেয়েছি। তা সে যা-ই হোক, ব্যতিক্রমের কথা ছেড়ে দিলে, মোটামুটি যে-নিয়মটা পাওয়া যায়, সেটা এই যে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে অক্ষর আর মাত্রার সংখ্যা সাধারণত সমান সমান; অর্থাৎ এর এক-এক লাইনে যত অক্ষর তত মাত্রা। শুধু তা-ই নয়, যুক্তাক্ষর যদিও শব্দের ওজন বাড়ায়, তবু অক্ষরবৃত্ত ছন্দের গণনাপদ্ধতি এতই সমদৰ্শী যে, যুক্তাক্ষরকে সে একমাত্রার বেশি মর্যাদা দেয় না।
মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে অক্ষরবৃত্তের প্রধান পার্থক্যটা এইখানেই। মাত্রাবৃত্তের বেলায় যে-নিয়মে আমরা এক-একটা লাইনের ধ্বনিপ্রবাহকে ভাগ করে মাত্রা গণনা করি, তাতে প্রতিটি অক্ষর তো এক-মাত্রার মূল্য পায়-ই, যুক্তাক্ষর পায় দু-মাত্রার মূল্য। (বলা বাহুল্য, সেই যুক্তাক্ষরটি শব্দের মধ্যে কিংবা অন্তে থাকা চাই, এবং সেই যুক্তাক্ষরের ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণটি হস্বৰ্ণ না-হওয়া চাই*; শব্দের আদিতে যুক্তাক্ষর থাকলে তার মাত্রাগত মূল্য বাড়ে না, সে তখন ধ্বনিগত ওজনের বিচারে আর পাঁচটা সাধারণ অক্ষরের তুল্যমূল্য। যুক্তস্বর ঐ” আর ‘ঔ’ –এর দাপট অবশ্য আরও কিছু বেশি। শব্দের আদি-মধ্য-অন্ত যেখানেই থাক, মাত্রাবৃত্তে তারা দু-মাত্ৰা আদায় করবেই।)
আসলে কথাটা এই যে, অক্ষরবৃত্ত ছন্দে উচ্চারণকে সংকুচিত ক’রে মাত্রার যোগফলে গোল না-ঘটিয়েও শব্দের ওজন বাড়িয়ে নেবার যে-সুবিধেটা পাওয়া যায়, মাত্রাবৃত্তে সেটা মেলে না। মাত্রাবৃত্তে যদি যুক্তাক্ষর ঢোকাই, তবে দু-মাত্রার মূল্য সে ঠিকই আদায় করে ছাড়বে। (অবশ্য— আবার বলি- সে যদি শব্দের মধ্যে কিংবা অন্তে থাকে এবং তার পূর্ববতী বর্ণটি যদি হিসাবর্ণনা হয়।) মাত্রার মাশুল ফাঁকি দিয়ে শব্দের ওজন বাড়াবার কোনও উপায়ই এক্ষেত্রে নেই। নীচের লাইন দুটি লক্ষ করুন :
আকাশে হঠাৎ দেখে একফালি চাঁদ
ছন্দের কামড়ে কবি হলেন উন্মাদ।
বলাই বাহুল্য, এই লাইন দুটি অক্ষরবৃত্ত ছন্দে লেখা। এর প্রথম লাইনে অক্ষরের সংখ্যা মোট চোদ্দো, যুক্তাক্ষর একটিও নেই, এবং মাত্রার সংখ্যাও মোট চোদ্দো। দ্বিতীয় লাইনে অক্ষরের সংখ্যা মোট চোদ্দো, তার মধ্যে দু-দুটি যুক্তাক্ষর, কিন্তু মাত্রার সংখ্যা। তবু চোদ্দে তো চোদ্দেই, তার এক কাচ্চাও বেশি নয়। অর্থাৎ যুক্তাক্ষরের জন্য সেখানে বাড়তি মাত্রার মাশুল গুনতে হয়নি।
মাত্রাবৃত্ত হলে কিন্ত এমনটি হতে পারত না। সেখানে যুক্তাক্ষর ঢোকালেই সে দু-মাত্রা মাশুল আদায় করে ছাড়ত। নীচের লাইন দুটি লক্ষ করুন।
যেই তিনি দেখেছেন একফালি চাঁদ
কবিবর হয়েছেন ঘোর উন্মাদ।
এ-দুটি লাইন মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা। প্রথম লাইনে অক্ষরের সংখ্যা মোট চোদ্দো, যুক্তাক্ষর একটিও নেই, এবং মাত্রার সংখ্যা মোট চোদ্দো। দ্বিতীয় লাইনে অক্ষরের সংখ্যা মোট তেরো, কিন্তু মাত্রার সংখ্যা। তবু চোদ্দো, তার কারণ তেরোটি অক্ষরের মধ্যে একটি হচ্ছে যুক্তাক্ষর, এবং সেই যুক্তাক্ষরটি দু-মাত্রা আদায় করে ছেড়েছে। হিসেবটা সুতরাং এই রকমের দাঁড়াল। বারোটি সাধারণ অক্ষর = ১২ মাত্রা; তৎসহ একটি যুক্তাক্ষর = ২ মাত্রা; মোট ১৪ মাত্রা। বাস্।
প্রশ্ন এই যে, যুক্তাক্ষরকে এখানে আমরা দু-মাত্রা দিচ্ছি কেন। উত্তর : দিতে বাধ্য হচ্ছি; ছন্দের চাল। নইলে ঠিক থাকে না। ছন্দের চাল ঠিক রাখবার জন্যেই যুক্তাক্ষরকে এখানে আমরা বিশ্লিষ্ট করছি; তাকে ভেঙে দুটি পৃথক অক্ষর হিসেবে পড়ছি। এবং সেইজন্যেই (অর্থাৎ তাকে ভেঙে দুটি পৃথক অক্ষর হিসেবে পড়ছি বলেই) তাকে দু-দুটি মাত্রা দিতে হচ্ছে।
,অক্ষরবৃত্ত আশ্লেষে স্মৃৰ্তি পায়, মাত্রাবৃত্ত বিশ্লেষে। অক্ষরবৃত্ত জোড়া দিতে চায়, মাত্রাবৃত্ত ভাঙতে। অক্ষরবৃত্তে শব্দের মধ্যবতী বিযুক্ত হস্বৰ্ণও অনেকসময়ে, দৃশ্যত না হোক, শ্রবণের ঔদার্যে তার পরবর্তী অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত হয়। যথা চার জন= চার্জন। মাত্রাবৃত্তে তার উলটো নিয়ম। সেখানে যুক্তাক্ষরকেও আমরা বিযুক্ত করে। পড়ি। যথা সার্জন= সারজন। অক্ষরবৃত্তে পোস্ট অফিসের চতুরক্ষর “ডাকতার’-বাবুটকেও প্রয়োজনবোধে কানের কাছে ত্রিবীর্ণ ‘ডাক্তার’ হিসেবে চালিয়ে দিয়ে ১-মাত্রা গাপ করা যায়। মাত্রাবৃত্তে কিন্তু খাঁটি ত্ৰিবৰ্ণ ‘ডাক্তার বাবুটিও ৪-মাত্রার কম ফি নেন না। কানের কাছে তিনিই তখনই চতুরক্ষর ডাক্তার বাবু। অক্ষরবৃত্তে ‘খাকতির খাই, দরকার হলে, ২-মাত্রার মূল্য দিয়েই মেটাতে পারি (কানের কাছে তিনি তখন খাঁক্তি); মাত্রাবৃত্তে ‘ভক্তি’র মতো বিশুদ্ধ হৃদয়বৃত্তিও ‘ভকতি’ হিসেবে শক্ত হাতে পুরো তিন মাত্ৰা আদায় করে ছাড়ে।
মাত্রাবৃত্তের এইটিই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। যুক্তাক্ষরকে সে যুক্ত থাকতে দেয় না, তাকে সে ভেঙে দেয়। এই জন্যেই এককালে একে যুক্তাক্ষর-ভাঙা ছন্দ বলা হত।
বাংলা কবিতায় যুক্তাক্ষরকে এইভাবে ভেঙে পড়বার কোনও সুনির্দিষ্ট রীতি আগে ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এই নতুন রীতির প্রবর্তক। প্রবর্তন ঘটল তাঁর মানসী-পর্বের কবিতায়। তার আগে যে তিনি কিংবা আর-কেউ যুক্তাক্ষরকে কদাচ ভেঙে ব্যবহার করেননি, এমন বলতে পারিনে, তবে ভাঙলেও সেটা আকস্মিক ঘটনা, তখনও সেই ভাঙাটা কোনও নির্দিষ্ট নিয়মের ব্যাপার হয়ে ওঠেনি। অর্থাৎ অক্ষরবৃত্তের জানলা দিয়ে মাত্রাবৃত্ত তখন এক-আধ বার এসে উকি দিয়ে যেত মাত্র, তার বেশি কিছু নয়। মানসী-তেই প্রথম দেখতে পাওয়া গেল যে, যুক্তাক্ষরকে ভেঙে ব্যবহার করবার প্রবণতা একটা নির্দিষ্ট, পরিকল্পিত নিয়মের বাঁধনে এসে ধরা দিয়েছে। সেই হিসেবে মানসী-তেই এই নতুন ছন্দের- মাত্রাবৃত্তের— সূচনা।
দেখতে পেলুম, মাত্রাবৃত্তের বেলায় আমরা যুক্তাক্ষরগুলিকে ভেঙে ভেঙে পড়ি। ছন্দের চাল নইলে ঠিক থাকে না। চালটাকে ঠিক রাখবার জন্যেই এক্ষেত্রে শব্দের ভিতরকার কিংবা শেষের যুক্তাক্ষরকে ভেঙে দুটি আলাদা-আলাদা অক্ষর হিসেবে গণ্য করতে হয়, এবং আলাদা-আলাদাভাবেই তাদের মাত্রার মাশুল চুকিয়ে দিতে হয়। (যুক্তস্বর ঐ কিংবা ঔ অবশ্য শব্দের আদিতে থাকলেও মাত্রাবৃত্তে দু-মাত্রার মর্যাদা পায়। সে-কথা আমরা আগেও বলেছি)। আমরা লিখি বটে শব্দ’, কিন্তু মাত্রার মূল্য দিতে গিয়ে তাকে ‘শবদ’রূপে গণ্য করি। আমরা দেখি বটে ‘অক্ষর’, কিন্তু মাত্রার মাশুল দেবার বেলায় তাকেই ‘অকখর হিসেবে দেখতে হয় (বিদ্বজ্জন অবশ্য ‘অক্ষর’ শুনলে আরও বেশি খুশি হবেন। কিন্তু আমরা তো আর বিদ্বজ্জন নই, তাই ‘অকখর’ শুনেই তুষ্ট থাকব।) আমরা ‘ছন্দ বিচার করতে গিয়ে মাত্রাবৃত্তের বেলায় তাকে ‘ছন্দ’ হিসেবে বিচার না করে পারি না।
অর্থাৎ চোদো মাত্রায় লাইন সাজিয়ে আমরা যখন লিখি;
ছন্দের গুতো খেয়ে পোড়োদের হায়
চোখ থেকে অবিরল অশু গড়ায়।
কহে কবিকঙ্কণ, ‘কান্না থামাও,
ক্লাস থেকে মানে-মানে চম্পট দাও।’
তখন যুক্তাক্ষরগুলিকে একে-একে ভেঙে-ভেঙে আমরা মাত্রার মাশুল চুকিয়ে দিই; ফলে লাইনগুলির চেহারা বস্তৃত এই রকমের দাঁড়ায় :
ছন্দের গুতো খেয়ে পোড়োদের হায়
চোখ থেকে অবিরল অশ্রু, গড়ায়।
কহে কবিকংকণ, ‘কান্না থামাও,
ক্লাস থেকে মানে-মানে চম্পট দাও।’
লক্ষ করুন, সর্বক্ষেত্রেই আমরা যুক্তাক্ষরকে ভেঙে দিয়েছি, ফলে ফি-লাইনে এখন চোদ্দোটি করে অক্ষর পাচ্ছি, এবং সেই চোদো অক্ষরের প্রত্যেকেই এক-একটি করে মাত্ৰা-মূল্য পাচ্ছে (ভাঙিনি শুধু একটি যুক্তাক্ষরকে; চতুর্থ লাইনের ‘ক্লাস’ শব্দের ‘ক্ল’-কে। এই ব্যতিক্রমের কারণ আপনার আগেই জেনেছেন। যুক্তাক্ষরটি এক্ষেত্রে শব্দের প্রথমেই রয়েছে; ফলে তাকে ভাঙা সম্ভব নয়। শব্দের প্রথমে আছে বলে মাত্রাবৃত্তেও সে এক-মাত্রার বেশি দাবি করবে না।)
আসলে ব্যাপারটা এই যে, মাত্রাবৃত্তের বেলায় হস্বর্ণগুলিকেও একটি করে মাত্রার মূল্য দিয়ে দিতে হয়। অক্ষরবৃত্তের ক্ষেত্রে শুধু বিযুক্ত হস্বর্ণগুলিকেই আমরা মাত্রার মূল্য দিই। (অনেকসময়ে তা-ও দিই না, বিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও তাদের মাত্রা আমরা দরকার হলেই গাপ করি); মাত্রাবৃত্তের বেলায় সেক্ষেত্রে বিযুক্ত হস্বর্ণগুলি তো মাত্রার মূল্য পায়ই, তদুপরি যেসব হিসাবর্ণ যুক্তাক্ষরের মধ্যে লুকোনো, মাত্রাবৃত্ত তাদেরও যুক্তাক্ষরের ভিতর থেকে টেনে বার করে আনে, এবং তাদের হাতেও একটি করে মাত্রার মূল্য ধরিয়ে দেয়। অক্ষরবৃত্তের কষ্ট’ (২-মাত্রা) তাই মাত্রাবৃত্তের কাছে কষট’ (৩-মাত্রা), অক্ষরবৃত্তের আনন্দ’ (৩-মাত্রা) তাই মাত্রাবৃত্তের কাছে ‘আননন্দ (৪-মাত্ৰা); অক্ষরবৃত্তের মহোল্লাস’ (৪-মাত্রা) তাই মাত্রাবৃত্তের কাছে মহোলালাস” (৫-মাত্রা)। এবং এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, অক্ষরবৃত্তের রাস্তা” আর মাত্রাবৃত্তের রাস্তা” মোটেই এক নয়। আর তাই মাত্রাবৃত্তকে আসলে মাতৃরাবৃত্ত লিখলেই ঠিক হত; ছা্ন্দসিকেরা তাতে নিশ্চয় বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট হতেন না!
আমরা বলেছি, মাত্রাবৃত্তের সূচনা মানসী পর্বের কবিতায়। মানসী-র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, “আমার রচনার এই পর্বেই যুক্ত অক্ষরকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে ছন্দকে নূতন শক্তি দিতে পেরেছি।” পূর্ণ মূল্য দেওয়ার অর্থ দুই মাত্রার মূল্য দেওয়া। বাংলা কবিতায় যুক্তাক্ষরকে ইতিপূর্বে দুই-মাত্রার মূল্য দেবার সুনির্দিষ্ট রীতি ছিল না। এখন যুক্তাক্ষরকে ভেঙে তাকে দুই-মাত্রার মূল্য দিয়ে দেখা গেল, ছন্দের চোলই একেবারে পালটে গেছে। ঘাড়ের উপর থেকে বাড়তি বোঝা নামিয়ে দেওয়ায় তার গতি অনেক বেড়ে গেছে; সে আর গজেন্দ্রগমনে চলতে চাইছে না।
উপমা দিয়ে বলতে পারি, অক্ষরবৃত্তের চাল যেন হাতির চাল; পিঠের উপরে যুক্তাক্ষরের বাড়তি বোঝা নিয়ে সে ধীরপায়ে এগোয়। আর মাত্রাবৃত্ত যেন তেজি ঘোড়ার মতো; সংকেত পেলেই সে যুক্তাক্ষরের শিকল ছিঁড়ে ঘাড় বেঁকিয়ে পায়ের খুরে হস্যবর্ণের খাটাখাট ধ্বনি বাজিয়ে ছুটতে থাকে।
মানসী-র দ্বিতীয় কবিতা ‘ভুল ভাঙা’। তার প্রথম স্তবকেই দেখছি :
“বাহুলতা শুধু বন্ধনপাশ
বাহুতে মোর।”
‘বন্ধন’কে ভেঙে এখানে চার-মাত্রার মূল্য দেওয়া হয়েছে। ছান্দসিক বলছেন, শুধু বাহুলতার বন্ধন কেন, বাংলা কবিতায় যুক্তাক্ষরের বন্ধনও এই একই সঙ্গে ভেঙে গেল।
অক্ষরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তের চাল যে একেবারে আলাদা, তা আমরা বুঝতে পেরেছি। কেন আলাদা তা-ও বুঝলুম। এখন, মাত্রাবৃত্তের আপনি এলাকার মধ্যে যেসব আলাদা আলাদা চাল রয়েছে, তার খবর নিতে হবে।
মাত্রাবৃত্তের চাল সাকুল্যে চার রকমের। ৪-মাত্রার চাল, ৫-মাত্রার চাল, ৬-মাত্রার চাল, আর ৭-মাত্রার চাল। অনেকে আবার ৮-মাত্রার চালের কথা বলেন। কিন্তু ৮-মাত্রার চাল যে একটা আলাদা জাতের চাল, এমন কথা মেনে নেওয়া শক্ত। শ্ৰীপ্ৰবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ও তাকে আলাদা জাতের চাল বলে মেনে নেননি। আসলে, হঠাৎ দেখলে যাকে ৮-মাত্রার চাল বলে মনে হয়, পর্ব ভাঙলে বুঝতে পারি যে, সেটা ৪-মাত্রারই একটা রকমফেরমাত্র, তাকে আলাদা একটা চাল বলাটা ঠিক নয়।
মূল কথায় ফিরে আসি। লাইনের এক-একটা অংশ কিংবা পর্বে মাত্ৰা-সংখ্যা কত, তারই হিসেব নিয়ে আমরা বলি, এটা অত-মাত্রার চাল, সেটা তত-মাত্রার। এবারে আসুন, মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এমনকিছু পদ্য বানাই, যার প্রতিটি পর্বের মাত্ৰা-সংখ্যা হচ্ছে চার।
কী নিয়ে পদ্য বানাব? সন্দেশ নিয়ে? বেশ, তা-ই হোক। ওই মহার্ঘ বস্তু মুখে তোলা যে জনসাধারণের পক্ষে কোনওকালেই খুব সহজ ছিল, এমন বলতে পারিনে, তবে চোখে অন্তত দেখা যেত। কিছুকাল আগে ছানার মিষ্টি নিষিদ্ধ হওয়ায় তা-ও যাচ্ছিল না। সেইসময়কার পটভূমিকায় সন্দেশ-বিষয়ক একটি পদ্য বানানো যাক। তা আমাদের তৎকালীন বেদনার কথাটাকে আমরা এইভাবে প্রকাশ করতে পারি। :
সন্দেশ চেখে দেখা ছিল সুকঠিন;
চোখে দেখা, তা-ও হল নিষিদ্ধ, তাই
চক্ষুতে আসে জল, তাই রাতদিন
সন্দেশ নিয়ে শুধু পদ্য বানাই।
পদটা বিশেষ জুতের হল না। না হোক, চালটা ঠিকই বুঝতে পারা যাবে। আরও ভালো করে বুঝবার জন্যে এই লাইন-কাটিকে পর্বে পর্বে ভাগ করে ফেলা যাক। ভাগ করলে এর চেহারাটা এই রকমের দাঁড়ায়–
সন্দেশ/চেখে দেখা/ছিল সুক/ঠিন;
চোখে দেখা,/তা-ও হল/নিষিদ্ধ/তাই
চক্ষুতে/আসে। জল/তাই রাত/দিন
সন্দেশ/নিয়ে শুধু/পদ্য বা/নাই।
দেখা যাচ্ছে, পদ্যটির এক-এক লাইনে আমরা তিনটি করে পর্ব (এবং সেইসঙ্গে লাইনের প্রান্তে একটি ভাঙা-পর্ব) পাচ্ছি, এবং প্রতি পর্বে পাচ্ছি। চারটি মাত্রা। মাত্রাবৃত্তের ফ্যামিলিতে এ হল ৪-মাত্রার চাল।
*
ফি-লাইনে যে তিনটি করেই পর্ব রাখতে হবে, এমন কোনও কথা নেই। পর্বের সংখ্যা আমরা ইচ্ছে করলেই কমাতে কিংবা বাড়াতে পারি। কিন্ত চারি-মাত্রার চালটা। তাতে পালটাবে না। আর ফি-লাইনের শেষে যে ওই ভাঙা-পর্বটি পাচ্ছি, ওর যে কী কাজ, তা আশা করি আর নতুন করে ব্যাখ্যা করতে হবে না। অক্ষরবৃত্ত নিয়ে আলোচনার সময়েই ভাঙা-পর্বের কাজের কথাটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। তবু, বাহুল্য হলেও আর-এক বার বলি যে, ওর কাজ আর-কিছুই নয়, এক লাইন থেকে অন্য লাইনে যাবার আগে পাঠককে ও একটু দাঁড় করিয়ে রাখে, তাকে একটু দম ফেলবার ফুরসত দেয়। তা সে যাই হোক, ভাঙা-পর্বটি এক্ষেত্রে ২-মাত্রার। ইচ্ছে করলে আমরা ১-মাত্রা কিংবা ৩-মাত্রার ভাঙা-পর্বও ব্যবহার করতে পারতুম।
৪-মাত্রার চালের আর-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। এবারে যে-পদ্য বানোব, তার ফি-লাইনে থাকবে ৪-মাত্রার দুটি করে পর্ব আর সেইসঙ্গে ১-মাত্রার একটি ভাঙা-পর্ব।
সাতপাঁচ ভাবিছটা কী,
কাজে লেগে যাও বাবুজি।
ভেবে ভেবে কুল পায় কে,
অকারণে ভ্ৰান্তি বাড়ে।
ভাবনার কোটি হাত-পা,
লাখো মাথা, প্ৰকাণ্ড হাঁ।
চিন্তার শেষ নেই তো।
চিন্তার নেই সীমানা,
সুতরাং চিন্তা না; না।
পর্ব ভাগ করে দেখলেই বোঝা যাবে যে, আমরা কথার খেলাপ করিনি; যে-নিয়মে লাইনে বাঁধব বলেছিলুম, ঠিক সেই নিয়মেই বেঁধেছি/ভাগ করে দেখালে আমাদের লাইনগুলির চেহারা এই রকমের দাঁড়ায় :
সাতপাঁচ/ভাবিছটা/কী,
কাজে লেগে/যাও বাবু/জি।
ভেবে ভেবে/কুল পায়/কে,
অকারণে/ভ্রান্তি বা/ড়ে।
ভাবনার/কোটি হাত-/পা,
লাখো মাথা/প্রকাণ্ডা/হাঁ।
থই পাবে/কই তার/জো,
চিন্তার/শেষ নেই/তো।
চিন্তার/নেই সীমা/না,
সুতরাং/চিন্তা না;/না।
গুনে দেখুন, এর ফি-লাইনে ৪-মাত্রার দুটি করে পর্ব আছে; আর সেইসঙ্গে আছে ১-মাত্রার একটি ভাঙা-পর্ব।
৪-মাত্রার চালের আর-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। এবারে আমাদের ফি-লাইনে থাকবে তিনটি করে পর্ব, আর ভাঙা-পর্বটি হবে ৩-মাত্রার। বিষয় : সূর্যগ্রহণ। পদ্যটিকে আমরা এইরকমে সাজাতে পারি। :
দিবার আজ বড়ো করুণার পাত্র
চক্ষু নিবেছে তার, আলো নেই আকাশে।
নিশানাথ-সাথে নেই ভেদ লেশমাত্র, সকালের পাগড়িতে যেন চাঁদ বাকী সে। পর্ব ভেঙে দেখলে এই লাইনগুলির চেহারা এই রকমের দাঁড়ায় :
দিবাকর/আজ বড়ো/করুণার/পত্র,
চক্ষুনি/বেছে তার/আলো নেই/আকাশে।
নিশানাথ/সাথে নেই/ভেদ লেশ/মাত্র,
সকালের/পাগড়িতে/যেন চাঁদ/বাঁকা সে।
অর্থাৎ ফি-লাইনে এখানে পর্ব আছে তিনটি করে। ভাঙা-পর্ব একটি। পর্বগুলি ৪-মাত্রার। ভাঙা-পর্বগুলিকে আমরা ৩-মাত্রার রেখেছি।
আর নয়। মাত্রাবৃত্তের এলাকায় ৪-মাত্রার চাল আমরা অনেক দেখলুম। এর পরে ৫-মাত্রার চাল দেখব। প্রসঙ্গত বলে রাখি, ভাঙা-পর্বের বৈচিত্ৰ্য আর দেখতে চাইনে। ছন্দের মূল চাল তো আর ভাঙা-পর্বের হ্রাসবৃদ্ধির উপরে নির্ভর করে না। সুতরাং তার উপরে জোর দিয়ে লাভ নেই।
***
পাঁচ মাত্রার চালের মাত্রাবৃত্তের প্রতি পর্বে থাকে পাঁচটি করে মাত্রা। তবে কান পাতলেই ধরা পড়বে যে, আমরা যাকে ৫ বলছি, বস্তৃত সে ৩ + ২। অর্থাৎ ৫-মাত্রার পর্ব আসলে ৩-মাত্রা আর ২-মাত্রার সমষ্টি; বিজোড়-জোড়ে তার শরীর গড়া।। ৪-মাত্রার ছন্দ এগোয় খটখট-খাটাখাট চালে; ৫-মাত্রার ছন্দ সেক্ষেত্রে খটাস-খাট খটাস-খাট ধ্বনি জাগিয়ে চলতে থাকে। নীচের লাইনগুলি লক্ষ করুন :
আসতে-যেতে এখনো তুলি চোখ,
রেলিঙে আর দেখি না নীল শাড়ি।
কোথায় যেন জমেছে কিছু শোক,
ভেঙেছ খেলা সহসা দিয়ে আড়ি।
এখন সব স্তবধ নিরালোক;
অন্ধকারে ঘুমিয়ে আছে বাড়ি।
এ হল ৫-মাত্রার চাল। এর প্রতি লাইনে আছে দুটি করে পর্ব (ইচ্ছে করলেই পর্ব আরও বাড়ানো যেত); আর সেইসঙ্গে একটি ভাঙা-পর্ব। পর্বগুলি ৫-মাত্রায় গড়া; ভাঙা-পর্বটি ২-মাত্রার। ভেঙে দেখলে এই লাইনগুলির চেহারা এইরকম দাঁড়ায় :
আসতে- যেতে/এখনো তুলি/চোখ,
রেলিঙে আর/দেখি না। নীল/শাড়ি।
কোথায় যেন/জমেছে কিছু/শোক,
ভেঙেছ খেলা/সহসা দিয়ে/আড়ি।
এখন সব/স্তবধ নিরা/লোক,
অন্ধকারে/ঘুমিয়ে আছে/বাড়ি।
৫-মাত্রার চালকে যে কেন ৩ + ২ মাত্রার চাল বলেছি, এখন আর সেটা বুঝতে কোনও অসুবিধে হবার কথা নয়। এ হল বিজোড় + জোড়, বিজোড় + জোড় চাল। মাত্রার হিসেবে শব্দগুলিকে যদি সেইভাবে (অর্থাৎ বিজোড়া + জোড়, বিজোড়’ + জোড় করে) সাজানো হয়, তবে তো কথাই নেই, ছন্দের নৌকো একেবারে তরতর করে চলবে; তবে মাঝে-মাঝে তার অন্যথা ঘটলেও (অর্থাৎ বিজোড়-মাত্রার বিজোড়-মাত্রার শব্দ বসালেও) তাতে কোনও ক্ষতি হয় না। কেন-না, জোড়-মাত্রার শব্দটি প্রথমে বসলেও, ছন্দের চালের তাড়নায়, সে পরবতী শব্দের প্রথম মাত্রাটিকে নিজের শরীরের মধ্যে টেনে আনে। (অর্থাৎ জোড়’ + বিজোড় তখন জোড়বি + জোড় হয়ে যায়।) দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। নীচের লাইনগুলি লক্ষ করুন :
দুপুর গেল, বিকেল হল সারা,
গোপনে ফোটে একটি-দুটি তারা,
বাতাসে যেন চাপা বেদনা লাগে।
বেদনা করি, কথাটা তার কী,
পৃথিবী তার কিছুই বোঝেনি;
আকাশে বাঁকা চন্দ্ৰকলা জাগে।
পর্ব ভেঙে দেখালে এই লাইনগুলির চেহারা এইরকম দাঁড়ায়।
দুপুর গেল,/বিকেল হল/সারা,
গোপনে ফোটে/একটি-দুটি/তারা,
বাতাসে যেন/চাপা বেদনা/লাগে।
বেদনা করি/কথাটা তার/কী,
পৃথিবী তার/কিছুই বোঝে/নি;
আকাশে বাঁকা/চন্দ্ৰকলা/জাগে।
এখানে প্রতিটি পর্বেই ৫-মাত্ৰা গড়া হয়েছে বিজোড় + জোড় বিজোড় + জোড় দিয়ে। শুধু একটি ক্ষেত্রে- তৃতীয় লাইনের চাপা বেদনায়- তার ব্যতিক্ৰম দেখছি। ‘চাপা বেদনা’ বিজোড় + জোড় নয়, জোড় + বিজোড়। কিন্তু তাতেও কিছু অসুবিধের সৃষ্টি হচ্ছে না। কেন না, বিজোড় + জোড় এই ছন্দের তাড়নাই তাকে ”চাপাবে দানা’ বানিয়ে ছাড়ছে।
আর-একটা ব্যাপারও লক্ষ করুন। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় আর ষষ্ঠ লাইনের অন্তে যে ভাঙা-পর্ব রয়েছে, তার প্রত্যেকটিই ২-মাত্রা দিয়ে গড়া। ব্যতিক্ৰম ঘটেছে চতুর্থ আর পঞম লাইনের প্রান্তবর্তী ভাঙা-পর্বে। ও-দুটি পর্ব ১-মাত্রার। দেখা যাচ্ছে, একই কবিতার মধ্যে এক-এক জায়গায় আমরা এক-এক রকমের ভাঙা-পর্ব গড়লুম, কিন্তু কানের তাতে আপত্তি নেই। আসলে, জায়গা বুঝে এইভাবে ব্যতিক্ৰম ঘটালে কান যেমন আপত্তি তোলে না, তেমনি কবিতার শরীরে কিছুটা বৈচিত্ৰ্যও আনা যায়। (বলেছিলুম, ভাঙা-পর্বের উপরে জোর দেব না। তবু যে একটু কারিকুরি করলুম, তার হেতুটা আর কিছুই নয়, লোভ। কারিকুরির সুযোগ পেয়ে আর ছাড়া গেল না।)
৫-মাত্রার চালের আর-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। লাইনের বিন্যাস এবারে একটু পালটে দেব। নীচের লাইনগুলি লক্ষ করুন :
কিছুটা ছিল অন্ধকার
কিছুটা ছিল আলো;
কিছুটা ছিল শুভ্ৰ, আর
কিছুটা ছিল কালো।
জীবনভোর জ্বলেছ। যার বিষে
ওষ্ঠে তার সুধাও ছিল মিশে।
এবারে তবে স্মরণে তার
নয়নে ক্ষমা জ্বালো–
কিছুটা ছিল মন্দ যার,
বাকিটা ছিল ভালো।
এবারে আর পর্ব ভেঙে দেখাচ্ছিনে। কষ্ট করে নিজেরাই ভেঙে নিন। তাহলে দেখতে পাবেন, এর পর্বগুলি ৫-মাত্রার। কোনও লাইনে দুটি করে পর্ব আছে, কোনও লাইনে একটি করে। কোথাও ভঙা-পর্ব আছে, কোথাও নেই। কিন্তু সব মিলিয়ে একটা প্যাটার্ন ঠিকই তৈরি হয়েছে।
৫-মাত্রার চাল দেখানো এখানেই শেষ হল।
***
পাঁচের পরে ছয়। মাত্রাবৃত্তের সংসারে এবারে ৬-মাত্রার চাল দেখবার পালা। এই চালে যদি চলতে হয়, তবে পর্বে-পর্বে ছটি করে মাত্রার বরাদ চাপাতে হবে। লাইনের শেষের ভাঙা-পর্বটি আমরা যেমন-খুশি গড়তে পারি।
ধরা যাক, আমরা অন্ত্রানের শীত নিয়ে দু-চার ছত্র লিখতে চাই। হঠাৎ বিষম ঠান্ডা পড়েছে, লেজ গুটিয়ে বাঘ পালাচ্ছে (ঈশ্বর জানেন পালায় কি না, কিন্তু কথাটা শোনাচ্ছে ভালো), খালবিল জমে কুলপি বরফ হয়ে যাচ্ছে (বলা বাহুল্য, বাংলা দেশে জমে না, কিন্তু লিখলে ক্ষতি কী, কবিতায় তো শুনতে পাই সাতখুন মাফ), গাছের ডালে একটা পাখি বসে থারথার করে কঁপিছে, কবিরা এই হাড়-কাঁপানো শীতের মধ্যে হাটেমাঠে মিল খুঁজে বেড়াক, কিন্তু গৃহস্থের পক্ষে এখন জানালা-দরোজা বেশ উত্তমরূপে এটে রাখা দরকার— এই হবে আমাদের বিষয়বস্তু। তা ৬-মাত্রার চালে এই কথাগুলিকে আমরা এইভাবে সাজাতে পারি :
অঘ্রান মাসে পড়েছে ঠান্ডা বড়ো
ব্যাঘ্র পালায়, জমে যায় খালবিল;
বৃক্ষশাখায় বসে কাঁপে থরোথরো
সঙ্গবিহীন বৃদ্ধ একটি চিল।
কবি, তুমি যাও, হাটেমাঠে খুঁজে মরো
দু-চারটে মন-মজানো কথার মিল;
গৃহস্থ, তুমি জানোলা বন্ধ করো,
দরোজায় বেশ ভালো করে আঁটো খিল।
এ-ও মাত্রাবৃত্ত, কিন্তু, পড়লেই বুঝতে পারবেন, ৪-মাত্রা কিংবা ৫-মাত্রার চালের সঙ্গে এর মিল নেই। এর চাল হচ্ছে ৬-মাত্রার। কানে শুনেও যদি কেউ তা না-বুঝে থাকেন, তবে পর্ব ভাঙলেই ব্যাপারটা তিনি চক্ষুষ উপলব্ধি করতে পারবেন। পর্ব ভাঙলে এই লাইনগুলির চেহারা এইরকম দাঁড়ায় :
অস্ত্ৰান মাসে/পড়েছে, ঠান্ডা/বড়ো,
ব্যাঘ্র পালায়,/জমে যায় খালি/বিল;
বৃক্ষশাখায়/বসে কাঁপে থরো/থরো
সঙ্গবিহীন/বৃদ্ধ একটি/চিল।
কবি, তুমি যাও,/হাটেমাঠে খুঁজে/মারো
দু-চারটে মন-/মজানো কথার/মিল;
গৃহস্থ তুমি/জানোলা বন্ধ/করো,
দরোজায় বেশী/ভাল করে আঁটো/খিল।
দেখতেই পাচ্ছেন, এর প্রতি লাইনে আছে দুটি করে পর্ব। (সেইসঙ্গে লাইনের প্রান্তে একটি করে ভাঙা-পর্ব রয়েছে)। আর প্রতি পর্বে আছে ছটি করে মাত্রা (ভাঙা পর্বগুলি দু-মাত্রার)। বলা বাহুল্য, পর্বের সংখ্যা আমরা ইচ্ছে করলেই আরও বাড়াতে পারতুম।
আর-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ধরা যাক, এবারে আমরা মাছ নিয়ে লিখব। তা বঙ্গদেশে আজ মাছ নিয়ে কিছু লেখা মানেই মাছ-না-থাকার কথা লেখা। মীনাভাবে হীন হয়ে আছি; না আছে ইলিশ, না আছে পাকা রুই: বাজারে ঢুকলে যেন কান্না পায়; নিষ্পাদপ ভূখণ্ডে বাঁটকুল এরণ্ডও যেমন দ্রুমের সম্মান পায়, ‘নির্মীন’ বঙ্গদেশে টিলাপিয়া তেমনি আজ ফাঁকতালে আসর জমাচ্ছে। তা এই কথাগুলিকে আমরা ৬-মাত্রার চালে এমননিভাবে সাজাতে পারি। :
ইলিশ, তোমাকে দেখি না,
শুধুই তোমার স্বপ্ন দেখে
সপ্তাহ-মাস-বৎসর যায়,
দুঃখে বিন্দরে হিয়া।
সান্ত্বনা দিতে নেই পাকা রুই,
সেও বহুকাল থেকে
নিখোঁজ, এখন বাজার জমায়
রাশি রাশি টিলাপিয়া।
লাইন আর মিলের বিন্যাসটা একটু অন্য রকমের বটে, কিন্তু এ-ও সেই ৬-মাত্রারই চাল। পর্ব ভাঙলে এই লাইনগুলির চেহারা এইরকমের দাঁড়াবে :
ইলিশ, তোমাকে/দেখি না,
শুধুই/ তোমার স্বপ্ন/দেখে
সপ্তাহ-মাস-/বৎসর যায়,/
দুঃখে বিন্দরে/হিয়া।
সান্ত্বনা দিতে/নেই পাকা রুই,/
সেও বহুকাল/থেকে
নিখোঁজ, এখন/বাজার জমায়/
রাশি রাশি টিলা/পিয়া।
দেখা যাচ্ছে, এর প্রথম, তৃতীয়, পঞম আর সপ্তম লাইনের শেষে ভঙা-পর্ব নেই বলেই সেখানে থেমে থাকা যাচ্ছে না, দ্রুত গিয়ে পরবর্তী লাইনে ঢুকতে হচ্ছে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ আর- বলাই বাহুল্য- শেষ লাইনের শেষে ভাঙা-পর্ব আছে বলে সেখানে আমরা দাঁড়াতে পারি। আসলে ব্যাপারটা এই যে, প্রথম লাইনের সঙ্গে দ্বিতীয় লাইনকে, তৃতীয় লাইনের সঙ্গে চতুর্থ লাইনকে, পঞম লাইনের সঙ্গে ষষ্ঠ লাইনকে, এবং সপ্তম লাইনের সঙ্গে অষ্টম লাইনকে আমরা অনায়াসেই জুড়ে দিতে পারতুম; পাঠের ব্যাপারে তাতে এতটুকু ইতারবিশেষ হত না।
আর-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। এবারে আমাদের বক্তব্যকে আর-একটু উচ্চস্তরে উঠিয়ে আনব। নীচের লাইনগুলি লক্ষ করুন :
যন্ত্রণা থেকে আনন্দ জেগে ওঠে
শোক সান্ত্বনা হয়;
কাঁটার ঊর্ধ্বে গোলাপের মতো ফোটে
সমস্ত পরাজয়।
এটাও যে ৬-মাত্রার চাল, সেটা বোঝাবার জন্য আশা করি আর পর্ব ভেঙে দেখাতে হবে না।
***
চার, পাঁচ আর ছায়ের চাল আমরা দেখেছি। এবারে ৭-মাত্রার চাল দেখবার পালা। মাত্রাবৃত্তের ঘরে এইটিই আপাতত চুড়ান্ত চাল। বাংলা কাব্যে এর দৃষ্টান্ত খুব বেশি নেই। চার, পাঁচ। আর ছয়ের তুলনায় ৭-মাত্রার চালে লেখা কবিতার সংখ্যা যে অনেক কম, তাতে সন্দেহ করিনে। ৭-মাত্রার দৃষ্টান্ত রবীন্দ্ৰকাব্যে কিছু আছে; রবীন্দ্রনাথের পরেও অনেকে মাত্রাবৃত্তের এই চালে কবিতা লিখেছেন; হাল-আমলের কবিরাও যে এ-চালে চলেন না, এমন নয়; তবে তার দৃষ্টান্ত খুব বেশি চোখে পড়ে না।
দেখা যাক, আমরা এ-চালে চলতে পারি কি না। নীচের এই লাইনগুলি লক্ষ করুন :
ছিল না উদ্যত জটিল জিজ্ঞাসা,
মুক্ত অবারিত চিত্তে ছিল আশা।
নদীর কলতানে
পাখির গানে-গানে
বিশ্ব ভরা ছিল, মধুর ছিল ভাষা,
তখন বুকে ছিল গভীর ভালোবাসা।
জানি না, ঠিক-চালে এই লাইনগুলিকে আপনারা পড়তে পেরেছেন কি না। না-পারলে তাতে লজ্জার কিছু নেই, বিস্ময়েরও না। কেন-না। হুট করে একটা নতুন চালে পা ফেলা খুবই শক্ত ব্যাপার; যেমন ছয়ে-চারে তেমনি সাতে-পাঁচে অনেকেরই গন্ডগোল বেধে যায়। পা যেখানে পড়বার কথা, তার কিছুটা আগে পড়লেই মুশকিল, সাতকে তখন পাঁচ বলে মনে হতে পারে। দ্বন্দু ঘুচিয়ে দেবার ওজন্যে প্রথমে এই লাইনগুলিকে পর্বে পর্বে ভাগ করে দেখানো যাক :
ছিল না উদ্যত/জটিল জিজ্ঞাসা,/
মুক্ত অবারিত / চিত্তে ছিল আশা।/
নদীর কলতানে/
পাখির গানে-গানে/
বিশ্ব ভরা ছিল/মধুর ছিল ভাষা,/
তখন বুকে ছিল/গভীর ভালোবাসা/
দেখতেই পাচ্ছেন, প্রথম দ্বিতীয় পঞম ও ষষ্ঠ লাইনের প্রত্যেকটিতে আছে দুটি করে পর্ব তৃতীয় ও চতুর্থ লাইনে আমরা একটি করে পর্ব রেখেছি; লাইনের শেষে ভাঙা-পর্ব রাখিনি (ইচ্ছে করলেই রাখতে পারতুম); প্রতিটি পর্বই ৭-মাত্রায় গড়া। মুশকিল। এই যে, ৭-মাত্রার এই পর্বগুলিকে যদি ৫+২ হিসেবে পড়েন, তাহলেই ধন্ধ। লাগবে, মনে হবে এ-ও (একটি পর্ব ও একটি ভাঙা-পর্ব সংবলিত)। ৫-মাত্রার চাল। ধন্ধ এড়াবার জন্য একে ৩+৪ হিসাবে পড়া দরকার। পর্বের প্রথমাংশ (অর্থাৎ ৩-মাত্রাকে) একসঙ্গে পড়ুন, অতঃপর দ্বিতীয়াংশ (অর্থাৎ বাকি ৪-মাত্রাকে) একসঙ্গে পড়ুন। দ্বিতীয়াংশের প্রথমে যেন একটু জোর পড়ে। তাহলে আর ভাবনা নেই; সাতে-পাঁচে গুলিয়ে না-ফেলে তখন স্পষ্ট বুঝতে পারবেন, অন্যান্য চালের সঙ্গে এর তফাতটা কোথায়। ফি-মাত্রাকে যদি একটি পদক্ষেপ বলে গণ্য করি, তো ৭-মাত্রার এই চালকে ‘সপ্তপদী চাল’ বললে কি অন্যায় হবে?
কে যেন বারে বারে তার
পুরোনো নাম ধরে ডাকে;
বেড়ায় পায়ে-পায়ে, আর
কাঁধের পরে হাত রাখে।
অথচ খাঁখাঁ চারিধার,
ঠান্ডা চাঁদ চেয়ে থাকে;
ও-হাতখানি। তবে কার,
কে তবে ডাক দিল তাকে?
৭-মাত্রার চালটাকে ধরতে পারা যাতে আরও সহজ হয়, তার জন্যে আর-একটু বিশদ করে, অর্থাৎ ৭-মাত্রাকে তিনে + চারে ভাগ করে, এবারে পর্ব ভাঙছি। শুধু তা-ই নয়, শব্দগুলিকে কোথাও জুড়ে দিয়ে, কোথাও ভেঙে দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি,
কেযেন + বারেবারে/ তার
পুরনো+নামধরে/ডাকে;
বেড়ায়ন-পায়েপায়ে/আর
কাঁধের+পরেহাতি/রাখে।
অথচ +খাঁখাঁচারি/ধার,
ঠান্ড+চাঁদচেয়ে/থাকে,
ওহাত-খানিতবে/কার,
কেতবে+ডাকদিল/তাকে?
বলা বাহুল্য, পর্বের শারীরিক গঠনটাকে স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্যেই এই অদ্ভুত পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছি। কবিতা পড়বার সময়ে এতটাই কসরত করবার দরকার নেই। করতে গেলে শুধু ছন্দই পড়া হবে, কবিতা পড়া হবে না। সে-কথা থাক। এবারে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে, ৭-মাত্রার চাল আসলে তিন+চারের যোগফল। এখানে ফি-লাইনে আছে ৭-মাত্রার একটি করে পর্ব ও তৎসহ দু-মাত্রার একটি করে ভাঙা-পর্ব। আশা করি, এর পরে আর ৭-মাত্রার চাল নিয়ে কারও ধন্ধ লাগবে না।
আরও একটি দৃষ্টান্ত তবু দিচ্ছি :
রাস্তা উঁচুনিচু, চলেছি সাবধানে,
বিশেষ নেই পুঁজিপাটা।
বিপদ চারিদিকে, বিঘ্ন সবখানে,
পথের সবখানে কাঁটা।
এবারে আর পর্ব ভেঙে দেখাব না। নিজেরাই ভেঙে নিন।
মাত্রাবৃত্তের আলোচনা, আপাতত, এখানেই শেষ হল। এ-ছন্দের নিয়মগুলি আপনারা জেনে নিয়েছেন। নিয়মের ব্যতিক্রমও নেহাত কম নেই। একটি ব্যতিক্রমের কথা এখানে বলি।
আমরা জেনেছি এবং দেখেছি যে, মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বেলায় শব্দের মধ্যে কিংবা অন্তে অবস্থিত যুক্তাক্ষর দু-মাত্রার মূল্য পায়। (যদি না সেই যুক্তাক্ষরের ঠিক পূর্ববতী বর্ণটি হয় হস্বৰ্ণ) যুক্তস্বর (ঐ, ঔ) অবশ্য- শব্দের মধ্যে কিংবা অন্তে থাকলে তো বটেই— আদিতে থাকলেও দু-মাত্রার মূল্য পেয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, শব্দের আদিতে যেখানে যুক্তস্বর, সেখানে সেই যুক্তস্বরের পাশে একটি যুক্তব্যঞ্জন থাকলে তারা দুয়ে মিলে ২+২=8 মাত্রার মূল্য আদায় করতে পারে না। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :
দৈন্যকে কেন আর সৈন্যে সাজাও,
চৈত্রে মৈত্রী চায় পাষণ্ডেরাও।
এখন, এই যে আমরা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে দু-লাইন লিখলুম, মাত্রাবৃত্তের নিয়ম অনুযায়ী ‘দৈন্য’ ‘সৈন্যে’ ‘চৈত্রে’ আর ‘মৈত্রী’- এই শব্দ চতুষ্টয়ের প্রত্যেকেরই তো এখানে চার-মাত্রার মূল্য পাবার কথা, কিন্তু তা তারা কেউ পাচ্ছে কি? কেউই পাচ্ছে না। প্রত্যেকেই পাচ্ছে তিন-মাত্রার মূল্য। প্রত্যেকেরই আদিতে আছে যুক্তস্বরের দাপট ও সেই যুক্তস্বরের ঠিক পাশেই আছে যুক্তব্যঞ্জনের দাবি। এবং এই দুয়ের সংঘর্ষে প্রতিটি শব্দের ক্ষেত্রে একটি করে মাত্ৰা মারা পড়ছে। ‘বৌদ্ধ’ ‘ঔদ্ধত্য” ইত্যাদি শব্দের বেলাতেও মাত্রাবৃত্তে একটি করে মাত্রা লোপ পেয়ে যায়। প্রশ্ন হছে, লোপ পেয়ে যায়। কার হিসসা থেকে? অর্থাৎ সংঘর্ষের ফলে কার শক্তিক্ষয় ঘটে? শব্দের আদিতে অবস্থিত যুক্তস্বরের, না তার পাশে বসা যুক্তব্যঞ্জনের? অনেকে বলবেন, আদির ওই যুক্তস্বরই এসব ক্ষেত্রে দুর্বল হয়ে পড়ে ও তার মাত্রা মূল্য কমে যায়। আবার অনেকে হয়তো বলবেন, না, সংঘর্ষের ফলে মার খাচ্ছে ওই পাশে-বসা যুক্তাক্ষরটিই। সেক্ষেত্রে কেউ-কেউ আবার এমনও বলতে পারেন যে, একটু-একটু মোর খাচ্ছে দুজনেই। এই তিন অভিমতের কোনটা ঠিক, সেটা ধ্বনিতাত্ত্বিকের বিচাৰ্য।**
কিন্তু না, আর নয়, মাত্রাবৃত্তের সীমানা পেরিয়ে এসেছি, এবারে আমরা স্বরবৃত্তের রাজ্যে ঢুকব।
—————
* শব্দের মধ্যে কিংবা অন্তে থাকা সত্ত্বেও যুক্তাক্ষর দু-মাত্রার মূল্য পায় না, যদি সেই যুক্তাক্ষরের পূর্ববতী বর্ণটি হয় হস্বৰ্ণ। দৃষ্টান্ত : ট্রানস্লেশন। এক্ষেত্রে যুক্তাক্ষরটি শব্দের মধ্যবর্তী হওয়া সত্ত্বেও— যেহেতু তার পূর্ববতী বর্ণটি হস্বৰ্ণ, তাই— দু-মাত্রার মূল্য পাচ্ছে না। মাত্রাবৃত্তেও না।
** ‘পরিশিষ্ট’-অংশে কবি শ্ৰীশঙ্খ ঘোষের চিঠি দেখুন।
০৬. স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্ত বা শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ
যেমন অক্ষরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তের ব্যাপারে নিয়েছি, তেমনি স্বরবৃত্তের ব্যাপারেও নাম-পরিচয়টা আগেই স্পষ্ট করে জেনে নেওয়া যাক। স্বরবৃত্ত নামটিও শ্ৰীপ্ৰবোধচন্দ্র সেনেরই উদভাবিত। তবে লৌকিক ছন্দ নামেও তিনি একেই বোঝাতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সেক্ষেত্রে এই ছন্দকে বলতেন বাংলা প্রাকৃত’। শ্ৰীঅমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বলেন শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দ। স্বরবৃত্ত নামটি পরে শ্ৰীপ্ৰবোধচন্দ্র সেনের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়। তিনি এর নতুন নাম রাখেন দলবৃত্ত। তবে পুরনো নামটা যখন প্রসিদ্ধি পেয়েই গেছে, তখন আমরা তাকে ছাড়ছিনে, এই আলোচনায় স্বরবৃত্ত নামটাই আমরা ব্যবহার করব।
এবারে সেই স্বরবৃত্তের রাজ্যে ঢোকার পালা। বলা বাহুল্য, মাত্রাবৃত্তের এলাকায় আমরা যেভাবে ঢুকেছিলুম, স্বরবৃত্তের এলাকাতেও ঠিক সেইভাবেই ঢুকব। অর্থাৎ কিনা গোত্তা মেরে দুম করে ঢুকব না। তার চাইতে বরং দূরে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণের জন্য তার চালচলন বেশ উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করব; বুঝে নেব, অক্ষরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে তার গতিভঙ্গিমার তফাত কোথায়। সেটা যদি ভালো করে বুঝতে হয়, তাহলে অক্ষরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তের পাশাপাশি রেখে তাকে দেখা দরকার। তাতে তুলনা করবার সুবিধা মেলে; বুঝতে পারি, কে কোনভাবে পা ফেলে হাঁটছে। ছন্দবিচারে অবশ্য দেখার মূল্য যৎসামান্য, শোনার মূল্যই বেশি। যার চলন দেখতে চাই, আসলে তাকে বাজিয়ে দেখতে হবে। আসুন, অক্ষরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্তকে তাহলে পাশাপাশি বাজিয়ে দেখা যাক।
ধরা যাক, আমরা ভোজনপর্ব নিয়ে কিছু লিখতে চাই। দিনকাল যা পড়েছে, তাতে সত্যি তো আর ভোজনের সাধ মেটাবার উপায় নেই, এখন শুধু পদ্য বেঁধেই শখ মেটাতে হবে। তা কথা এই যে, শখটা তিন রকমের ছন্দেই মেটাতে পারি। প্রথমত লিখতে পারি :
দক্ষিণহস্তের ক্রিয়া জমে পরিপাটি
পলান্নের সঙ্গে পেলে কোমা এক বাটি।
বুঝতেই পারছেন, এ হল অক্ষরবৃত্ত ছন্দ। ছন্দ পালটে এবারে আর-এক রকমের দোলা লাগিয়ে এই কথাগুলিকে প্রকাশ করা যাক। লেখা যাক :
দাও যদি পলান্ন, সাথে এক বাটি
কোর্মা দিলেই
ভোজনের পর্বটা জমে পরিপাটি–
সন্দেহ নেই।
এ হল মাত্রাবৃত্ত ছন্দ। (চালটা এক্ষেত্রে ৪-মাত্রার) এবারে পুনশ্চ ছন্দ পালটে এই কথাগুলিতে আমরা আর-এক রকমের দোল লাগাব। লিখব :
আহার জমে পরিপাটি
সত্যি বলি ভাই
পলান্ন আর একটি বাটি
কোর্মা যদি পাই।
এ হল স্বরবৃত্ত। অক্ষরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তের পাশাপাশি একে পড়ুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন যে, এর চলন একেবারে আলাদা।
আবার দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এবারে কী নিয়ে লিখব? ফুর্তির কথা তো লিখলুম, এবারে অন্য-কিছু লেখা যাক। বক্তব্যকে আর-একটু উঁচুতে উঠিয়ে এনে, আসুন, হৃদয়ঘটিত কিছু লিখি। পর-পর তিন রকমের ছন্দে সে-কথা লেখা হবে।
(১) অক্ষরবৃত্ত
ঘৃণায় বিঁধেছ যাকে,
ঘৃণায় বিঁধেছে যাক, দিয়েছ ধিক্কার
দিয়েছ ধিক্কার আহবান জানালে তাকে মিথ্যে কেন আর?
(২) মাত্রাবৃত্ত (৫-মাত্রা)
ঘৃণাতে যাকে বিধেছ, যাকে
বলেছ শুধু ছি-ছি,
সহসা কেন এখানে তাকে
ডেকেছ মিছিমিছি?
(৩) স্বরবৃত্ত
ঘৃণা করো যে লোকটাকে
শুধুই বলো ছি-ছি,
আবার তুমি কেন তাকে
ডাকলে মিছিমিছি?
দেখতেই পাচ্ছেন, মোটামুটি একই কথাকে আমরা তিন রকমের ছন্দে বাঁধিলুম। পাশাপাশি এদের বারিকয়েক পড়ে দেখুন। পড়তে গেলেই বুঝতে পারবেন, তৃতীয় ছন্দটির অর্থাৎ স্বরবৃত্তের চাল আগের দুটির কোনওটির সঙ্গেই মেলে না। এর পা ফেলবার ভঙ্গি একেবারেই আলাদা।
আবার দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। উদর থেকে যখন হৃদয়ে একবার প্রোমোশন পেয়েছি, তখন বক্তব্য নির্বাচনে আর সহসা আমরা লঘুচিত্ততার পরিচয় দিচ্ছিনে। ধরা যাক, কোনও-এক খণ্ডিতা নায়িকার নিরুদ্ধ বেদনার কথাকে আমরা প্রকাশ করতে চাই। তা তিন রকমের ছন্দেই সে-কথা প্রকাশ করা চলে। যদি অক্ষরবৃত্তে প্ৰকাশ করতে হয়, তো আমরা লিখব :
মুখে তার কথা নেই, শয্যার উপরে
সমস্ত না-বলা কথা অশ্রু হয়ে ঝরে।
চাল পালটে যদি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে এই কথাগুলি জানাতে হয়, তো সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি। :
মুখে কথা নেই ভীরু নায়িকার,
বিনিদ্র বিছানায়
না-বলা কথার যন্ত্রণা তার
অশ্রুতে ঝরে যায়।
এ হল ছয়ের চালের মাত্রাবৃত্ত। আবার এই একই কথাকে আমরা স্বরবৃত্তের সুতোতেও গেথে তুলতে পারি। সেক্ষেত্রে আমরা লিখব :
একটি কথা নেই মুখে তার
সঙ্গিবিহীন ঘরে
রুদ্ধ কথার যন্ত্রণাভার
অশ্রু হয়ে ঝরে।
অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্তের চাল যে সম্পূর্ণ পৃথক, আশা করি সেটা ইতিমধ্যে নিঃসংশয়ে বুঝে নিয়েছেন। এই পার্থক্যের মূলে রয়েছে এদের নিজস্ব গঠনরীতি। তাকে বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়বে, এদের চলন কেন আলাদা।
অক্ষরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তের গঠনরীতি ইতিপূর্বেই আমরা বিশ্লেষণ করেছি। করে একটা মোটামুটি নিয়মের হদিস পেয়েছি। সেটা এই যে, ১) অক্ষরবৃত্তে সাধারণত প্রতিটি অক্ষর একটি করে মাত্রার মূল্য পায়, এবং ২) মাত্রাবৃত্তে প্রতিটি অক্ষর তো একটি করে মাত্রার মূল্য পায়ই, প্রতিটি যুক্তাক্ষর (যদি সেই যুক্তাক্ষর শব্দের আদিতে না থাকে, কিংবা শব্দের মধ্যে অথবা অন্তে থাকলেও তার পূর্ববর্তী বর্ণটি যদি হস্বৰ্ণ না হয়) পায় দু-মাত্রার মূল্য।
স্বরবৃত্তে সেক্ষেত্রে প্রতিটি সিলেবলকে একটি করে মাত্রার মূল্য চুকিয়ে দিতে হয়।
সিলেবল-এর বাংলা প্রতিশব্দ কী করব? সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত করেছিলেন ‘শব্দ-পাপড়ি’, কালিদাস রায় করেছেন ‘পদাংশ’; প্ৰবোধচন্দ্ৰ ‘দল’-এর পক্ষপাতী। ‘পাপড়ি’ আর দল’-এর অর্থ একই। অনুমান করতে পারি, সত্যেন্দ্রনাথ আর প্ৰবোধচন্দ্ৰ শব্দকে পুষ্প হিসেবে দেখেছেন; সিলেবল তার পাপড়ি কিংবা দল। (কট্টর নৈয়ায়িকেরা সম্ভবত এইটুকু শূনেই ভুকুটি করে বলে বসবেন যে, শব্দকোশে সেক্ষেত্রে আর যে-পুষ্পেরই থাক, শতদলের দৃষ্টান্ত মিলবে না, কেন-না, একশসিলেবল দিয়ে যার অঙ্গ গড়া, এমন শব্দ না ভুতো ন ভবিষ্যতি)
কিন্তু সে-কথা পরে। সিলেবলই বলি, কিংবা পাপড়ি অথবা দলই বলি, বস্তুটা আসলে কী, আগে সেটা বোঝা চাই।
এক কথায় বলতে পারি, কোনও-কিছু উচ্চারণ করতে গিয়ে নূ্যনতম চেষ্টায় যেটুকু আমরা বলতে পারি, তা-ই হচ্ছে একটি সিলেবল। সেই দিক থেকে এক-একটি সিলেবল হচ্ছে আমাদের উচ্চারণের এক-একটি ইউনিট কিংবা একক। এই এককগুলির সমবায়েই আমাদের উচ্চারণের শরীর গড়ে ওঠে। দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্ছি :
ধরা যাক, কবিকঙ্কণ’ শব্দটাকে আমরা উচ্চারণ করতে চাই। করলুম। করে দেখতে পাচ্ছি, চারটি এককে তার অঙ্গ গড়া। আলাদা করে সেগুলিকে এইভাবে দেখানো যায় :
ক+বি+কং+কণ্
অর্থাৎ ‘কবিকঙ্কণ’ শব্দটি মোট চারটি সিলেবল-এর সমবায়ে গড়ে উঠেছে।
এই হিসেবে ছন্দ’ শব্দটিতে আছে দুটি সিলেবল (ছন + দ); আবারঅক্ষরের সংখ্যা যদিও বাড়ল— ‘বন্ধন’ শব্দটিতে দুটির বেশি সিলেবল নেই (বন। + ধন)।
এই পর্যন্ত যা বলেছি, তার থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সিলেবল দু-রকমের হতে পারে। ইংরেজিতে বলে ‘ওপন সিলেবল ও ‘ক্লোজড্ সিলেবল। প্ৰবোধচন্দ্ৰ তো সিলেবল শব্দটার বাংলা করেছেন দল, সেই হিসেবে ‘ওপন সিলেবল ও ‘ক্লোজড্ সিলেবলকে তিনি “মুক্তদল” ও “বুদ্ধিদল’ বলেন। ‘কবিকঙ্কণ’ শব্দটার মধ্যে “ক” আর ‘বি’ হচ্ছে মুক্ত সিলেবল; অন্য দিকে কিং’ আর ‘কৰ্ণ হচ্ছে রুদ্ধ। বুদ্ধ’ বলছি। এইজন্যে যে, “ক” আর ‘বি’-র মতো এ-দুটি সিলেবল-এর উচ্চারণকে টেনে নিয়ে যাওয়া যায় না। ‘ভাই’ বউ” “যাও” ইত্যাদিও বুদ্ধ সিলেবল-এর দৃষ্টান্ত। এসব “সিলেবল-এর শেষে যদিও স্বরবর্ণ আছে, তবু— উচ্চারণ যেহেতু তন্মুহুর্তেই ফুরিয়ে যায়, তাই- কাৰ্যত সেই স্বরবর্ণগুলি হসন্ত বর্ণেরই সামিল, ফলে এরাও বুদ্ধ সিলেবল বলে গণ্য হয়। ( যায়’, ‘হায়’ ইত্যাদির ক্ষেত্রে তো সেই এক কথা বটেই, “যাঃ’ বাঃ”, ইত্যাদিও রুদ্ধ সিলেবল।)
ইতিপূর্বে বলেছি, স্বরবৃত্ত ছন্দে সিলেবল-এর হিসেবে মাত্রার মূল্য চুকিয়ে দিতে হয়; ফি সিলেবলকে দিতে হয় একটি করে মাত্রার মূল্য। সেক্ষেত্রে এই রীতিতে দেখা যাচ্ছে মাত্রা-সংখ্যার দিক থেকে ‘ছন্দ” আর ‘বন্ধন” তুল্যমূল্য শব্দ; কেন-না অক্ষর-সংখ্যায় পৃথক হয়েও সিলেবল সংখ্যায় তারা সমান, তাদের দুজনেরই শরীর দুটি করে সিলেবল দিয়ে গঠিত হয়েছে।
অক্ষরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তের সঙ্গে স্বরবৃত্তের প্রধান পার্থক্য এইখানেই। ধ্বনিটাই অবশ্য প্রধান কথা, অক্ষর নেহাতই গৌণ ব্যাপার। সে-কথা আগেও অনেক বার বলেছি, তবু, প্রথম দুটি ছন্দের ক্ষেত্রে অক্ষরও একেবারে ন-গণ্য নয়। ব্যতিক্রমের কথা যদি ছেড়ে দিই, তবে অক্ষরের ভিত্তিতেও মাত্রার একটা মোটামুটি হিসেব সেখানে রাখা চলে। স্বরবৃত্তে সেটা একেবারেই চলে না। একই শব্দ যে এই তিন রকমের ছন্দে কীভাবে তিন রকমের মাত্রা মূল্য পায়, কবিকঙ্কণের কিঙ্কণ” দিয়েই সেটা বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে।
১) অক্ষরবৃত্তে সাধারণত প্রতিটি অক্ষরই একটি করে মাত্রার মূল্য পায়। সুতরাং “কঙ্কণ” সেখানে ৩-মাত্রার শব্দ।
২) মাত্রাবৃত্তে আমরা সাধারণত প্রতিটি অক্ষরকে একটি করে মাত্রার মূল্য দিই কিন্তু শব্দের মধ্যস্থ কিংবা প্রান্তবতী যুক্তাক্ষরকে (যদি না সেই যুক্তাক্ষরের ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণটি হয় হস্বৰ্ণ) দিই ২-মাত্রার মূল্য। সুতরাং কঙ্কণ” সেখানে ৪-মাত্রার শব্দ।
৩) স্বরবৃত্তে আমরা প্রতিটি সিলেবলকে একটি করে মাত্রার মূল্য দিই, এবং ‘কঙ্কণ’ শব্দটিতে মোট দুটি সিলেবল (কং+কণ) পাওয়া যাচ্ছে। সুতরাং কঙ্কণ’ সেখানে ২-মাত্রার শব্দ।
অর্থাৎ কিনা একই শব্দ তিন রকমের ছন্দে তিন রকমের মাত্রা মূল্য পাচ্ছে।
পদ্যের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা আরও পরিষ্কার হবে। পরপর তিন রকমের ছন্দে আমরা মোটামুটি একই বক্তব্যকে এখানে উপস্থিত করছি :
১) অক্ষরবৃত্ত
অঙ্কের দাপটে কাব্য নাভিশ্বাস ছাড়ে,
আনন্দের লেশ নেই ছন্দের বিচারে।
২) মাত্রাবৃত্ত (৬-মাত্রা)
অঙ্কের চোখ-রাঙানিতে হায়,
নাড়ি ছাড়ে কাব্যের,
ছন্দ-বিচারে বলো কেবা পায়
স্পর্শ আনন্দের?
৩) স্বরবৃত্ত
অঙ্ক কষে কিছু পেলে?
কাব্য গেল মারে।
আনন্দের কি পরাশ মেলে
ছন্দ-বিচার করে?
কথাটা সত্যি নয়। ছন্দ-বিচারেও আনন্দ মেলে। বইকি। আপাতত লক্ষ করে। দেখুন, “আনন্দের’ শব্দটি তিনটি দৃষ্টান্তেই আছে। কিন্তু তিন জায়গায় তার মাত্রা মূল্য সমান নয়। প্রথম দৃষ্টান্তে (অর্থাৎ অক্ষরবৃত্তে) সে পাচ্ছে ৪-মাত্রার মূল্য; দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে (অর্থাৎ মাত্রাবৃত্তে) সে পাচ্ছে ৫-মাত্রার মূল্য; আবার তৃতীয় দৃষ্টান্তে (অর্থাৎ স্বরবৃত্তে) সে মাত্র ৩-মাত্রার মূল্য পেয়েই খুশি থাকছে।
স্বরবৃত্তে সে মাত্র ৩-মাত্রার মূল্য পাচ্ছে কেন? কারণটা আগেই বলেছি। পাচ্ছে, তার কারণ, স্বরবৃত্তে মাত্রার মূল্য দেওয়া হয় সিলেবল অনুযায়ী, এবং ‘আনন্দের শব্দটিতে (আ+নন°দের) তিনটির বেশি সিলেবল নেই।
এবারে আমরা স্বরবৃত্তের পর্ব-বিভাগ করে দেখাব। সিলেবল অনুযায়ী মাত্রার মূল্য দেবার ব্যাপারটা তাতে আরও স্পষ্ট হবে। কিন্তু পর্ব ভেঙে দেখাবার জন্যে একটা পদ্য চাই। হাতের কাছে পদ্যের বই পাচ্ছিনে; তাই, আসুন, স্বরবৃত্ত ছন্দে লেখা লাইন-কয়েকের একটা টুকরো পদ্য নিজেরাই বানিয়ে নেওয়া যাক। ভয় পবার কিছু নেই, অক্ষরবৃত্ত আর মাত্রা বৃত্ত ছন্দে তো আর আমরা কম পদ্য বানাইনি, কান যদি ঠিক থাকে তো স্বরবৃত্তেও কয়েকটা লাইন আমরা ঠিকই খাড়া করে ফেলতে পারব।
ধরা যাক, আমাদের বক্তব্য এই হবে যে, রেলের কামরায় অকস্মাৎ এক পুরোনো বন্ধুর (কিংবা বান্ধবীর) সঙ্গে দেখা হয়েছে, খানিক বাদেই আবার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে, দুজনে দু-পথে চলে যাব, কিন্তু সেই বিচ্ছেদের ভাবনাকে আমরা আমল দিতে চাইনে, বরং দু-দণ্ডের এই হঠাৎ-মিলনকে গল্পে-গল্পে ভরিয়ে তুলতে চাই। তা স্বরবৃত্তে সেই কথাটাকে আমরা এইভাবে প্রকাশ করতে পারি :
পথের মধ্যে হঠাৎ দেখা,
ট্রেনের মধ্যে আলাপচারি;
স্টেশন এলেই আবার একা
অন্য পথে দেব পাড়ি।
সেটা সত্যি, কিন্তু অত
ভেবে দেখলে কষ্ট বড়ো;
বরং এসো, আপাতত
হালকা কিছু গল্প করো।
যাক, লাইনগুলি মোটামুটি খাড়া হয়েছে। এবারে একে পর্বে-পর্বে ভাগ করতে হবে। সেক্ষেত্রে এর চেহারা দাঁড়াবে এইরকম :
পথের মধ্যে/হঠাৎ দেখা,/
ট্রেনের মধ্যে/আলাপচারি;/
স্টেশন এলেই/আবার একা/
অন্য পথে/দেব পাড়ি।/
সেটা সত্যি,/কিন্তু অত/
ভেবে দেখলে/কষ্ট বড়ো;/
বরং এসো,/আপাতত/
হালকা কিছু/গল্প করো।/
দেখতে পাচ্ছি, এখানে ফি-লাইনে আছে দুটি করে পর্ব (সংখ্যাটাকে ইচ্ছে করলেই বাড়ানো যেত); লাইনের শেষে ভঙা-পর্ব নেই। (ইচ্ছে করলেই রাখা যেত)।
লাইন তো ভাঙলুম। এখন পর্বকেও যদি ভেঙে দেখি, তাহলে তার মধ্যে চারটি করে সিলেবল-এর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রথম লাইনের প্রথম পর্বটিকে ভেঙে দেখছি, প + থেরন্ + মধ্য + ধে- এই চারটি সিলেবল-এ তার শরীর গড়া। অন্য ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হবে না, যে-কোনও পর্ব এখানে ভাঙি না কেন, মোট চারটি করে সিলেবলই তাতে মিলবে।
এবং আপনারা আগেই জেনেছেন যে, স্বরবৃত্ত ছন্দে প্রতিটি সিলেবল একটি করে মাত্রার মূল্য পায়। সেই হিসেবে আমরা বলতে পারি যে, স্বরবৃত্তের চাল ৪-মাত্রার। মাত্রাবৃত্ত অনেক চালে চলে। কিন্তু স্বরবৃত্তের এই একটিই চাল। চারের চাল ছাড়া সে চলে না।
আর-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। এবারে আমাদের বিষয়বস্তু হবে ভালোবাসা। একটি মেয়ের চাউনিতে আলো জুলেছে, হাসিতে রং ধরেছে, অথচ ভঙ্গিটি সলজ। তার বুকের মধ্যে জেগেছে অসম্ভবকে জয় করবার আশা; অন্য দিকে, দ্বিধা আর ভয়ের শিকলটাকেও সে ছিড়তে পারছে না। অর্থাৎ কিনা সে প্রেমে পড়েছে। তা তার এই অবস্থােটাকে আমরা, স্বরবৃত্ত ছন্দে এইভাবে প্রকাশ করতে পারি :
দুটি চোখে কে ওই আলো জ্বালে,
ঠোঁটে লাগায় হাসি?
ভঙ্গিতে কে আমন করে ঢালে
লজ্জা রাশিরাশি?
বুকের মধ্যে বাজায় গুরুগুরু
অসম্ভবের আশা;
ভয়ে তবু কাঁপে যে তার ভুরু,
সেই তো ভালোবাসা।
ঈশ্বর জানেন, প্রথম-প্রেমের এই বর্ণনাটা সকলের মনঃপূত হল কি না। তবে এ-ও যে স্বরবৃত্তই, তাতে সন্দেহ নেই। পর্ব ভেঙে দেখালে এর চেহারা হবে। এইরকম :
দুটি চোখে/কে ওই আলো/জ্বালে,
ঠোটে লাগায়/হাসি?
ভঙ্গিতে কে/অমন করে/ঢালে
লজ্জা রাশি/রাশি?
বুকের মধ্যে/বাজায় গুরু/গুরু
অসম্ভবের/আশা;
ভয়ে তবু/কাঁপে যে তার/ভুরু,
সেই তো ভালো/বাসা।
দেখতে পাচ্ছি, এর প্রথম, তৃতীয়, পঞম আর সপ্তম লাইনে আছে দুটি করে পর্ব; দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ আর অষ্টম লাইনে সেক্ষেত্রে একটি করে পর্ব আছে। ফি-লাইনের শেষে আমরা ভাঙা-পর্ব রেখেছি। প্রতিটি পর্বই ৪-মাত্রায় গড়া (অর্থাৎ প্রতিটি পর্বেই চারটি করে সিলেবল আছে)। ভাঙা-পর্বগুলি ২-মাত্রার।
আরও একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। এবারে আমাদের বিষয়বস্তু হচ্ছে অকৃতজ্ঞতা।
প্রেম-ভালবাসা-প্রকৃতির কথা তো অনেক বললুম, এবারে জীবনের অন্ধকার দিকটার দিকেও একবার তােকানো যাক। যুগপৎ অকৃতজ্ঞ ও নির্বোিধ এমন মানুষের কথা বলা যাক, নিজের ক্ষমতার দৌড় না-বুঝেই যে কিনা উপকারীকে দংশন করতে উদ্যত :
চেহারাটা আজকে তোমার
এক মুহুর্তে পড়ল ধরা।
হাঁড়ির মধ্যে আটকা ছিলে,
যেই না খুলে দিলুম সরা–
অমনি তুমি আমার দেহেই
সমস্ত বিষ ঢালতে চাচ্ছ,
সাপের মতোই ফণা তুলে
দিব্যি তুমি ফোঁসফোঁসাচ্ছ।
কৃতজ্ঞতা কিছু নেই কি?
বুদ্ধি? তা-ও না? আরো ছি-ছি।
বুদ্ধি থাকলে বুঝতে পারতে
ভয় দেখাচ্ছ মিছিমিছি।
সাপের ওষুধ আছে আমার,
কোরো না তাই বাড়াবাড়ি।
তোমার মতন হাজার সাপকে
হাঁড়িতে ফের পুরতে পারি।
এবারে আর পর্ব ভেঙে দেখাচ্ছিনে। নিজেরাই ভেঙে নিন। ভাঙলে দেখতে পাবেন, এর ফি-লাইনে দুটি করে পর্ব আছে (লাইনের শেষে ভঙা-পর্ব নেই)। প্রতি পর্বে, যথারীতি, আছে চারটি করে সিলেবল।
কথা এই যে, স্বরবৃত্ত ছন্দে ৪-সিলেবল-এর পর্বটাই নিয়ম বটে, তবে মাঝে-মাঝে তার ব্যতিক্রমও ঘটে যায়। আমরা তিনটি মুক্ত ও একটি বুদ্ধ সিলেবল-এর সমবায়ে পর্ব গড়তে পারি (দৃষ্টান্ত : “দিনের আলো” = দি/নের/আ/লো), কিংবা চারটি মুক্ত সিলেবল-এর সমবায়ে পর্ব গড়তে পারি (দৃষ্টান্ত : ‘নিভে এলো”= নি/ভে/এ/লো), কিংবা দুটি মুক্ত ও দুটি বুদ্ধ সিলেবল-এর সমবায়েও পর্ব গড়তে পারি (দৃষ্টান্ত : “বাইরে কেবল” = বাই/রে/কে/বল)। এই সবই চার-সিলেবল-সম্পন্ন পর্বের দৃষ্টান্ত। কিন্তু সবগুলি সিলেবলকেই যদি বুদ্ধ রাখতে ইচ্ছা করি, তাহলে পর্বের মধ্যে সাকুল্যে তিনটির বেশি সিলেবল ঢোকাতে গেলে আমাদের ঘাম ছুটে যাবে। (দৃষ্টান্ত দেবার জন্যে এক্ষুনি একটা লাইন বানিয়ে নেওয়া যাক। “শনশন শন ৰাতাস বইছে”— এই যে লাইনটি, এর মধ্যে দুটি পর্ব আছে। “শন শন শন” আর “বাতাস বইছে”। তার মধ্যে প্রথম পর্ব অর্থাৎ “শন শন শন”-এর সব কটি সিলেবলই যেহেতু বুদ্ধ তাই সেই পর্বের মধ্যে সাকুল্যে তিনটির বেশি সিলেক্ল-এর জায়গা মেলেনি; মেলানো শাস্তু।) তাহলেই দেখা যাচ্ছে: ৪-মাত্রার নিয়মটা সর্বদা বজায় থাকে না; সিলেবল-এর চরিত্র অনুযায়ী মাত্রার সংখ্যা বাড়ে কমে। এখানে যে-দৃষ্টান্ত দিয়েছি, তা ছাড়া অন্য প্রকারের ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তও এই ছন্দে বিস্তর মেলে। যেমন মাত্রাহাস, তেমনি মাত্রাবৃদ্ধির দৃষ্টান্তও প্রচুর। স্বরবৃত্তের আর-এক নাম ছড়ার ছন্দ। তা চোখ বুলোলেই ধরা পড়বে যে, সেকাল আর একালের অনেক ছড়ারই অনেক পর্বে চারটি করে সিলেবল নেই। কোথাও বেশি আছে, কোথাও কম।
স্বরবৃত্ত ছন্দে একালেও কিছু কম কবিতা লেখা হয়নি। কিন্তু একালের কবিরাই যে পর্বে-পর্বে চারটি করে সিলেবল-এর বরাদ্দ চাপাবার কানুন সর্বদা মান্য করছেন, এমনও বলতে পারিনে। ব্যতিক্রম বিস্তর চোখে পড়ে। আকছার দেখতে পাই, পর্বে কোথাও সিলেবল-এর সংখ্যা চারের বেশি, কোথাও কম। সিলেবল-এর সংখ্যা যখন বাড়ে, তখন পাঁচে, এমনকি এক-আধ ক্ষেত্রে ছয়েও গিয়ে পৌছোয়। (প্রাচীন ছড়ায় ছয়-সিলেবলযুক্ত পর্বের দৃষ্টান্ত : কাজিফুল কুড়োতে কুড়োতে’ পেয়ে গেলাম মালা) যখন কমে, তখন সাধারণত তিনে এসে নামে।
ওঠানামার ব্যাপারটা কি কবিদের ইচ্ছাকৃত? অর্থাৎ চার-সিলেবল দিয়ে স্বরবৃত্তের পর্ব গড়বার যে একটি অলিখিত বিধান রয়েছে, সেইটোকে লঙ্ঘন করবার জন্যেই কি তাঁরা মাঝে-মাঝে সিলেবল-এর সংখ্যা বাড়ােন কিংবা কমান? উত্তরটা কবিরাই দিতে পারবেন। আমরা শুধু এইটুকু বলতে পারি যে, নিয়ম লঙ্ঘন করলেও র্তারা সাধারণত এক-পায়ের বেশি লঙ্ঘন করেন না। চারের সীমানা ছাড়িয়ে যখন তারা ওপরে ওঠেন, তখন বড়োজের এক পা ওঠেন। এবং যখন নামেন, তখন সাধারণত এক পা-ই নামেন। (নামতে নামতে দুয়ে নামবার দৃষ্টান্তও কিছু আছে।)
সীমানা ছাড়িয়ে ওপরে উঠবার দৃষ্টান্ত আগেই দেওয়া যাক। বিখ্যাত কিছু পদ্য কিংবা ছড়া থেকে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। (হাতের কাছে বই না থাকায় মিলিয়ে নেবার উপায় নেই। উদ্ধৃতিতে যদি একটু-আধটু ভুল ঘটে যায়, সহৃদয় পাঠক আশা করি ক্ষমা করবেন।) নীচের লাইন দুটি লক্ষ করুণ।
“রাত পোহাল, ফরসা হল, ফুটল কত ফুল;
কাঁপিয়ে পাখা নীল পতাকা জুটল। অলিকুল।”
এখানে ফি-লাইনে আছে তিনটি করে পর্ব। লাইনের শেষে ভঙা-পর্বও আছে। প্রতিটি পর্বে চারটি করে সিলেবল থাকবার কথা। আছেও। শুধু দ্বিতীয় লাইনের প্রথম পর্বে ব্যতিক্ৰম ঘটেছে। পর্বটি হল “কাঁপিয়ে পাখা’। হিসেব করে দেখুন, সিলেবল-এর সংখ্যা এক্ষেত্রে চার নয়, পাঁচ।
আর-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :
“জাদুর গুণের বালাই নিয়ে মরে যেন সে কাল!”
এটিও আপনাদের চেনা লাইন। এতেও আছে তিনটি পর্ব আর একটি ভাঙা-পর্ব। কিন্তু তৃতীয় পর্বে (‘‘মরে যেন সে) সিলেবল রয়েছে চারের বদলে পাঁচটি।
আর-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় :
“যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে।”
—এ-লাইনটিও আপনারা অনেক বার শুনেছেন। কিন্তু এর প্রথম পর্বে (যমুনাবতী) যে পাঁচটি সিলেবল রয়েছে, তা হয়তো সবাই খেয়াল করে দেখেননি। ঠিক তেমনি, ‘পূজাবাটীতে জোর কাঠিতে যখন ঢাক বাজে, তখনও অনেকেই খেয়াল করে দেখেন না যে, ‘পূজাবাটীতে” পুরো পাঁচটি সিলেবল গিয়ে ঢুকেছে।
ইতিপূর্বে আমরা স্বরবৃত্তের যেসব দৃষ্টান্ত নিজেরা তৈরি করে নিয়েছিলুম, তাতে অবশ্য কুত্ৰাপি কোনও ব্যতিক্রম ছিল না। কিন্তু থাকলেই কি তাতে স্বরবৃত্তের পবিত্রতা নষ্ট হত? ট্রেনের মধ্যে হঠাৎ-দেখতে-পাওয়া বন্ধুটির সঙ্গে খানিকবাদেই ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবে, এই কথাটা জানিয়ে আমরা লিখেছিলুম :
সেটা সত্যি, কিন্তু অত
ভেবে দেখলে কষ্ট বড়ো।
সেক্ষেত্রে ভেবে না-দেখে আমরা যদি তলিয়ে দেখতুম, এবং লিখতুম :
সেটা সত্যি, কিন্তু অত
তলিয়ে দেখলে কষ্ট বড়ো।
তাহলেই ব্যতিক্ৰম ঘটত, এবং দ্বিতীয় লাইনের প্রথম পর্বে (তালিয়ে দেখলে) পাঁচটি সিলেবল ঢুকে পড়ত। কিন্তু স্বরবৃত্তের চাল যে তাই বলে নষ্ট হত, এমন মনে হয় না।
নষ্ট হয় না সিলেবল-এর সংখ্যা কমে গেলেও। উর্ধ্বগতির কথা তো বললুম। নিম্নগতির ক্ষেত্রেও সেই একই কথা। চারের বদলে তিন সিলেবল দিয়েও মাঝেমাঝে স্বরবৃত্তের পর্ব গড়া হয়েছে, কিন্তু ছন্দের রেলগাড়ি তাতে বেলাইন হয়নি। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :
“আজ রামের অধিবাস কাল রামের বিয়ে।”
এটিও একটি সুপরিচিত লাইন, এবং এ-ও স্বরবৃত্তই। লাইনটিতে মোট তিনটি পর্ব, আর তৎসহ একটি ভাঙা-পর্ব রয়েছে। কিন্তু তিনটি পর্বের প্রত্যেকটিই এখানে তিন-সিলেবল দিয়ে গড়া (আজ রামের/অধিবাস/কাল রামের)।
আর-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :
“গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।”
এটিও একটি পরিচিত ছড়ার লাইন। এরও দ্বিতীয় পর্বে (ভাই আমার) আর তৃতীয় পর্বে (মন কেমন’) আছে তিনটি করে সিলেবল।
আরও একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। এবারে দু-লাইন নিজেরাই বানিয়ে নিচ্ছি :
রাতদিন তুই ছাইভস্ম কী যে
কথা বলিস নিজের সঙ্গে নিজে।
লাইন দুটির প্রত্যেকটিতে আছে দুটি করে পর্ব আর একটি করে ভাঙা-পর্ব। লক্ষ করে দেখুন, প্রথম লাইনের দুটি পর্বই (রাতদিন তুই/ছাইভস্ম), গড়া হয়েছে তিনটি করে সিলেবল দিয়ে।(1) কিন্তু ছন্দ তাতে বেচাল হয়নি।
কেন হয় না? সিলেবল-এর সংখ্যা চারের জায়গায় বেড়ে গিয়ে পাঁচ, কিংবা কমে গিয়ে তিন, হওয়া সত্ত্বেও কী করে ছন্দের চাল ঠিক থাকে?
ব্যাপারটার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ছান্দসিকেরা বলেন, চাল নষ্ট হয় না। আমাদের উচ্চারণের গুণে। (বললুম। ‘গুণ, কিন্তু ব্যাপারটা আসলে উচ্চারণের ‘দোষ” ছাড়া আর কিছু নয়। তবে এক্ষেত্রে সেটা দোষ হৈয়াও গুণ হচ্ছে বটে!)। আমরা লিখি বটে ‘কাঁপিয়ে পাখা’, কিন্তু উচ্চারণে সেটা ‘কাঁপ্য়ে পাখা’ হয়ে দাঁড়ায়, ‘তলিয়ে দেখলে’ হয় ‘তলয়ে দেখলে’। ফলে সিলেবলও একটি করে কমে যায়। কাঁপিয়ে পাখায় যেক্ষেত্রে পাঁচটি সিলেবল পাচ্ছি (কঁ+পি+য়ে পাখা), “কাঁপিয়ে পাখায় সেক্ষেত্রে চারটি সিলেবল মিলবে (কাঁপি+য়ে পা খা)। তলিয়ে দেখলে যেক্ষেত্রে পাঁচটি সিলেবল দিয়ে গড়া (ত+লি+য়ে দেখ+লে), তিলয়ে দেখলের সিলেবল সংখ্যা সেক্ষেত্রে চারের বেশি নয়। (তল-য়ে দেখ+লে)।
কিন্তু যমুনাবতীর ব্যাখ্যা কী? ছান্দসিকেরা এক্ষেত্রেও সম্ভবত বলবেন যে, তাড়াতাড়ি বলবার সময়ে আমরা ‘যমুনাবতী’ বলি না, বলি ‘যোম্নাবতী’; ফলে সিলেবল-এর সংখ্যা এক্ষেত্রেও চারে এসে দাঁড়ায় (যেমন-না–ব+তী)। এই নিয়ম অনুযায়ী মরে যেন সে’ আর ‘পূজাবাটীতে’র ক্ষেত্রেও সিলেবল-এর সংখ্যা কমে গিয়ে চারে এসে দাঁড়াবার একটা-কিছু ব্যাখ্যা নিশ্চয় মিলবে।
ব্যাখ্যা মেলে সিলেবল-এর সংখ্যা যেখানে চারের কম, সেখানেও। ছান্দসিক বললেন, তিন সিলেবলকেই আমরা সেখানে টেনে উচ্চারণ করে চারে এনে দাঁড় করাই। “আজ রামেরা/অধিবাস/কাল রামের/বিয়ে” এই লাইনটিকে টেনে বলি “আ-জ রামেরা/অধি-ব্যাস/কা-ল রামের/বিয়ে’। ‘গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করেীর ক্ষেত্রে প্রথম পর্বটিতে চারটি সিলেবল থাকায় টেনে পড়বার দরকার হয় না, কিন্তু দ্বিতীয় পর্বে আর তৃতীয় পর্বে সিলেবল-এর ঘাটতি থাকায় টেনে পড়তে হয়। ঘাটতি মেটাবার জন্যে বলতে হয়, “ভা-ই আমার/ম-ন কেমন”।
সিলেবল-এর সংখ্যা, আমরা আগেই আভাস দিয়েছি, তিনে নেমেই সর্বদা ক্ষান্ত হয় না। মাঝে-মাঝে, নামবার ঝোকে, সে দুয়ে গিয়েও নামে। প্ৰবোধচন্দ্র তার ছন্দ-পরিব্রুমা গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন :
“বাইরে কেবল/জলের শব্দ/ঝুপ ঝুপ/ঝুপ
দস্যি ছেলে/গল্প শোনে/একেবারে/চুপ।”
এখানে দুটি লাইনেই আছে তিনটি করে পর্ব ও একটি করে ভাঙা-পর্ব। প্রতি পর্বে আছে চারটি করে সিলেবল।। ব্যতিক্রম ঘটেছে শুধু প্রথম লাইনের তৃতীয় পর্বে। সিলেবল-এর সংখ্যা সেখানে শুধু যে কমেছে তা নয়, কমে একেবারে দুয়ে এসে ঠেকেছে। ছন্দের চাল তবু যে নষ্ট হয়নি, তার ব্যাখ্যা কী? ব্যাখ্যা অবশ্যই এই যে, ‘ঝুপ ঝুপকে এক্ষেত্রে আমরা টেনে “ঝুউপ-ঝুউপ” করে উচ্চারণ করি; ফলে চারের হিসেবটাও মিলে যায় (ঝু-উপ-কু-উপ), ছন্দের চালও নষ্ট হয় না।
স্বরবৃত্ত ছন্দের নিয়ম কী, আমরা জেনেছি। নিয়মের ব্যতিক্রমের কথাও জানলুম। ব্যতিক্ৰম ঘটা সত্ত্বেও ছন্দের চাল কেন নষ্ট হয় না, সেই ব্যাখ্যাটাও পাওয়া গেল। ব্যাখ্যা র্যােরা দিয়েছেন, তারা প্ৰবীণ ছান্দসিক। ছন্দশাস্ত্রে তারা পারদ্রষ্টা। তাদের পাণ্ডিত্য প্রশ্নাতীত; ধ্বনি ও উচ্চারণের হাড় হদ তারা জানেন। তাদের কথার প্রতিবাদ করব, এত বড়ো ধৃষ্টতা আমাদের নেই।
কিন্তু নিজেদের কথাটাকে জানাবার অধিকার নিশ্চয়ই আছে। আমাদের বক্তব্য আমরা এখানে পেশ করলুম।
১) “কাঁপিয়ে পাখ’, ‘তলিয়ে দেখলে’, ‘যমুনাবতী’, ‘মরে যেন সে, ‘পূজাবাটীতে’-জাতীয় পাঁচ সিলেবল সংবলিত পর্বের ক্ষেত্রে উচ্চারণকে কিছুমাত্র বিকৃত কিংবা সংকুচিত না করে (অর্থাৎ প্রতিটি শব্দকেই যথাবিধি উচ্চারণ করে) দেখেছি, স্বরবৃত্তের চাল তাতেও নষ্ট হয় না। ঠিকই থাকে।
২) তৎসত্ত্বেও যদি ছান্দসিকেরা বলেন যে, না, চাল ঠিক থাকে না, এবং ঠিক রাখবার জন্যেই উচ্চারণকে কোথাও (পর্বে যেখানে সিলেবল-এর সংখ্যা চারের বেশি) গুটিয়ে আনতে হবে, আবার কোথাও (পর্বে যেখানে সিলেবল-এর সংখ্যা চারের কম) ছড়িয়ে দিতে হবে, এবং পর্বের দৈর্ঘ্যে এইভাবে সমতা বিধান করতে ৩বে, তাহলে আমরা বিনীতভাবে প্রশ্ন করব যে, উচ্চারণের এইভাবে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটাবার রীতি তো গানের ব্যাপারে চলে, ও-রীতি কি কবিতাতেও চলা উচিত?
কথাটা যখন উঠলই, তখন আরও মূলে গিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। জিজ্ঞেস করা যায়, স্বরবৃত্ত ছন্দে উচ্চারণকে প্রয়োজনবোধে কোথাও গুটিয়ে আনা এবং কোথাও ছড়িয়ে দেওয়া (এবং এইভাবে পর্বের দৈর্ঘ্যে সাম্যবিধান করা) যদি অত্যাবশ্যক ৩য়ই, তবে স্বরবৃত্তকে মূলত কবিতার ছন্দ বলে গণ্য করা চলে কি না।(2)
প্রশ্নটা অকারণ নয়। আমরা সকলেই জানি, সেকালের অনেক ছড়াই গানের সগোত্ৰ। ঘুমপাড়ানি ছড়া তো বটেই। “খোকা ঘুমোল পাড়া জুড়োল বগি এল দেশে”— কোলের উপরে ছেলেকে শুইয়ে একালের জননীরাও যখন এই কথাগুলি উচ্চারণ করেন তখন অজান্তেই এই কথাগুলিতে কিছুটা সুরের দোলানি লেগে যায়। (প্রসঙ্গত বলি, “খোকা ঘুমোল’ আর ‘পাড়া জুড়োল’তেও সিলেবল-এর সংখ্যা চারের বেশি।) লাগে আরও অনেক ছড়াতেই। তখন মনে হয়, এই ছড়াগুলি আসলে কবিতা নয়, গান— যা সুর সহযোগে গেয়। কথার ভূমিকা সেখানে যৎসামান্য, সুরই সেখানে ছন্দ ঠিক রাখে। (সেই সুর হয়তো খুবই এলিমেনটারি, কিন্তু তা সুরই।) আর তা-ই যদি হয়, ছড়ার কথাগুলিকে তবে কবিতার ছন্দের কড়া-ইন্ত্রি নিয়মকানুনের ফ্রেমে আঁটাবার চেষ্টা কি কিছুটা অর্থহীন হয়ে পড়ে না? কাব্যছন্দের ব্যাকরণ দিয়ে তো গীতিকা-র শরীরকে আমরা বিশ্লেষণ করতে পারিনে।
ছান্দসিকেরা এ-সম্পর্কে কী বলবেন, আমাদের জানা নেই। তবে স্বরবৃত্তের চালচলন দেখে সন্দেহ না-হয়েই পারে না যে, এই ছন্দ মূলত গানেরই ছন্দ, পরবর্তী কালে কবিতাতেও যার সার্থক ব্যবহার সম্ভব হয়েছে।
—————
1. রাতদিন তুই’-পর্বটির তিনটি সিলেবলই বুদ্ধ, সুতরাং ইচ্ছে করলেও ওখানে অতিরিক্ত কোনও সিলেবল ঢোকানো শক্ত হত। “ছাইভস্ম’ পর্বটি সম্পর্কে কিন্তু সে-কথা খাটে না। ওখানে আছে দুটি বুদ্ধ ও একটি মুক্ত সিলেবল (ছাই+ভস+স)। সুতরাং আর-একটি সিলেবল ওখানে ঢোকানো যেত। কিন্তু তা না-ঢোকানো সত্ত্বেও যে ছন্দ বেচাল হয়নি, এটুকু অবশ্যই লক্ষণীয়।
2. ‘পরিশিষ্ট’ অংশে ড. ভবতোষ দত্তের চিঠি দ্রষ্টব্য।
০৭. সব ছন্দই কি সিলেবিক
যা বলবার বলেছি। এখন ছন্দের এই ব্যাপারটাকে আর-এক দিক থেকে দেখা যাক। তিন ছন্দের শারীরিক নির্মাণের উপরে নজর রেখে ভাবা যাক যে, এদের মাত্রা বিচারের কোনও সামান্য কৌশল আছে কি না। সামান্য বলতে এখানে তুচ্ছ কিংবা নগণ্য বোঝানো হচ্ছে না। ইংরেজিতে যাকে বলে “কমন, সামান্য এখানে তা-ই। (দৃষ্টান্ত : ইংরেজদের মধ্যে কেউ রোগা, কেউ মোটা, কেউ ঢাঙা, কেউ বেঁটে, কিন্তু এসব বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও তাদের যে একটা কমন ফ্যাকটর’ বা ‘সামান্য লক্ষণ” সকলের চোখে পড়ে, সেটা এই যে, তারা সবাই দিব্যি গৌরবরন।) এবং “সামান্য কৌশল’ বলতেও আমরা সেই কৌশলকে বোঝাচ্ছি, তিনটি ছন্দের মাত্রাবিচারেই যা প্রয়োগ করা যেতে পারে।
কিংবা ‘সামান্য কৌশল না-বলে আমরা মাসটার কী’ও বলতে পারি। স্বৰ্গত দীনেন্দ্ৰকুমার রায় ইংরেজি এই ‘মাস্টার কীর ভারী সুন্দর একটি বাংলা করে। দিয়েছিলেন। “সবখোলাচাবি”। কথা হচ্ছে, অক্ষরবৃত্ত মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্ত, এই তিন তালাকেই যা খুলতে পারে, এমন কোনও সবখোল চাবির আশা কি নেহাতই দুরাশা?
মোটেই নয়। সবখোল সেই চাবি আমাদের সামনেই রয়েছে। একটু লক্ষ করলেই আমরা দেখতে পাব যে, স্রেফ সিলেবল-এর চাবি ঘুরিয়েই আমরা তিন
মাত্রার ব্যাপারে, শুধু স্বরবৃত্ত নয়, তিনটি ছন্দই আসলে সিলেবল-এর উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে তারা পরস্পরের সগোত্র। অন্যদিকে, তাদের অমিলটা এইখানে যে, তাদের তিন জনের নির্ভরশীলতা তিন রকমের। যথা, স্বরবৃত্তে যেক্ষেত্রে সিলেবলমাত্রেই অনধিক একটি মাত্রার মূল্য পেয়েই খুশি, মাত্রাবৃত্তে সে-ক্ষেত্রে মুক্ত সিলেবল এক মাত্রার মূল্য পেলেও বুদ্ধ সিলেবল মূল্য পায়। দু-মাত্রার। আবার অক্ষরবৃত্তেও (ঠিক ওই স্বরবৃত্ত আর মাত্রাবৃত্তেরই মতো) প্রতিটি মুক্ত সিলেবলকে আমরা এক-মাত্রার মূল্য দিই বটে, কিন্তু বুদ্ধ সিলেবল-এর ক্ষেত্রে আরও-একটু ব্যতিক্ৰম ঘটে যায়।
স্বরবৃত্তে কী মুক্ত, কী বুদ্ধ, কোনও সিলেবলই এক-মাত্রার বেশি মূল্য দাবি করে না; মাত্রাবৃত্তে সেক্ষেত্রে বুদ্ধ সিলেবল সর্বত্র দু-মাত্রা দাবি করে; আর অক্ষরবৃত্তে সেক্ষেত্রে রুদ্ধ সিলেবল কোথাও এক-মাত্রা দাবি করে, কোথাও দু-মাত্রা।
প্রশ্ন : অক্ষরবৃত্তে বুদ্ধ সিলেবল কোথায় এক-মাত্ৰা দাবি করে এবং কোথায় তাকে দু-মাত্রার মূল্য দিতে হয়?
উত্তর : বুদ্ধ সিলেবল যেক্ষেত্রে শব্দের আদিতে কিংবা মধ্যে যুক্তাক্ষরের আশ্রয় নিয়ে নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে রাখে, সেক্ষেত্রে সে এক-মাত্রার বেশি মূল্য দাবি করে না; কিন্তু যুক্তাক্ষরের আশ্রয় নিয়েও যেক্ষেত্রে সে শব্দের অন্তে অবস্থিত, কিংবা শব্দের আদিতে বা মধ্যে অবস্থিত হয়েও যেক্ষেত্রে সে যুক্তাক্ষরের আশ্রিত নয়, সেক্ষেত্রে সে দু-মাত্রার মূল্য চায়।
দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। উদ্বন্ধন’ শব্দটি তিনটি বুদ্ধ সিলেবল দিয়ে গড়া। উদ-বন +ধন। কিন্তু তাদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় বুদ্ধ সিলেবল (উদ, বন) যেহেতু যুক্তাক্ষরের আশ্রিত, এবং যেহেতু তাদের প্রথম জনের (উদ) অবস্থান শব্দের আদিতে ও দ্বিতীয় জনের (বন) অবস্থান শব্দের মধ্যে, অতএব অক্ষরবৃত্তে তাদের কেউই এক-মাত্রার বেশি মূল্য চায় না। তৃতীয় জন (ধন) সেক্ষেত্রে যুক্তাক্ষরের আশ্রিত হয়েও শব্দের অন্তে রয়েছে। ফলত অক্ষরবৃত্তে সে দু-মাত্রার মূল্য দাবি করবে। এবং সব মিলিয়ে উদ্বন্ধন’ শব্দটি অক্ষরবৃত্তে পাবে চার-মাত্রার মূল্য (১+১+২)।
যাই হোক, মাত্রা-বিচারের ব্যাপারে দেখা যাচ্ছে সব ছন্দেই সিলেবল নামক ব্যাপারটার ভূমিকা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাই বলেই কি দুম করে আমরা বলে বসব যে, সব ছন্দই আসলে সিলেবিক? না, তা নিশ্চয় বলব না। শুধু বলব যে, সিলেবিক ছন্দে অর্থাৎ স্বরবৃত্তে তো সিলেবলকে ভুলে থাকবার কথাই ওঠে না, উপরন্তু ছন্দটা যেখানে স্বরবৃত্ত নয়, সেখানেও সিলেবলকে ভুলে থাকবার উপায় নেই।
০৮. পয়ার ও মহাপয়ার
ছন্দ নিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আলোচনার সময়ে লক্ষ করেছি, ‘পয়ার’ শব্দটিকে তাদের কেউ কেউ খুব শিথিলভাবে প্রয়োগ করেন। বস্তৃত, তাদের কাছে ‘পয়ার’ ও ‘অক্ষরবৃত্ত’ সমার্থক শব্দ; যখন তাঁরা বলেন যে, অমুক কবির হাতে পয়ার খুব ভালো খোলে, তখন আসলে তাঁরা বলতে চান যে, সেই কবি অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ব্যবহারে খুব দক্ষ। পয়ার ও অক্ষরবৃত্তে র্তারা এইভাবে তালগোল পাকিয়ে ফেলেন কেন, সেটা বোঝা অবশ্য শস্তু নয়। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের আলোচনায় ইতিপূর্বে আমি বলেছি, “রবীন্দ্রনাথের আগে পর্যন্ত, এমনকি রবীন্দ্ৰকাব্যেরও সূচনাপর্বে, বাংলা কবিতা প্রধানত অক্ষরবৃত্তে লেখা হয়েছে।” এখন বলি, অক্ষরবৃত্তে রচিত সেইসব কবিতার একটি মস্ত বড়ো অংশই পয়ারবন্ধে বাঁধা। খুবসম্ভব তারই ফলে অক্ষরবৃত্ত বলতে অনেকে পয়ার বোঝেন, এবং পয়ার বলতে অক্ষরবৃত্ত। কিন্তু পয়ার বলতে সত্যিই কোনও ছন্দ বোঝায় না, পয়ার আসলে একটা বন্ধমাত্র (অর্থাৎ কবিতার পঙক্তিবিন্যাসের বিশেষ একটা পদ্ধতি), এবং সেই বন্ধে যেমন অক্ষরবৃত্ত, তেমনই মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্তের পঙক্তিকে বাঁধা যেতে পারে। অনেকেই বেঁধেছেন।
কী সেই বন্ধের চেহারা? উত্তরটা সত্যেন্দ্ৰনাথ দত্ত দিয়েছেন। তিনিও অবশ্য পয়ার বলতে আলাদা একটা ছন্দই বুঝতেন (“পয়ার জান না? তুমি যে ছন্দে লিখেছি একেই বলে পয়ার”-‘ছন্দসরস্বতী’), কিন্তু তা হোক, ওই যে তিনি পয়ারের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখছেন “আট-ছয় আট-ছয় পয়ারের ছাঁদ কয়”, ওইটেই হচ্ছে পয়ার-বন্ধের সঠিক বর্ণনা। আট-ছয় বলতে এখানে আট-ছয় মাত্রার বিন্যাস বুঝতে হবে। অর্থাৎ যে-সব পঙক্তি আমাদের পড়বার ঝোক অনুযায়ী দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। (অংশ’ না বলে “পদ” বলাই রীতিসম্মত, কিন্তু পড়ুয়াদের বোঝাবার সুবিধার জন্য আপাতত আমি অংশ’ বলাই শ্রেয় মনে করছি, পদ-এর প্রসঙ্গ এর পরের পরিচ্ছেদে আসছে) এবং যার প্রথমাংশে পাওয়া যায় আটটি মাত্রা ও দ্বিতীয়াংশে ছটি, তাদেরই আমরা বলি পয়ার-বন্ধে বাঁধা পঙক্তি। এখন এই অংশভাগের কথাটা আর-একটু পরিষ্কার করে বলা দরকার। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে, পাঠকের দম নেবার সুবিধের জন্যে পঙক্তির শেষে একটা ভাঙা-পর্ব রাখা হয়, এবং সেই ভাঙা-পর্ব অনেকসময়ে দু-মাত্রার হয়। অক্ষরবৃত্ত ছন্দ নিয়ে আলোচনার সময়ে আমি এ-ও বলেছিলুম যে, কবিতার “লাইনটাকে যখন একসঙ্গে দেখি, তখন গোটা লাইনের বিন্যাসের মধ্যে ওই বাড়তি মাত্রা দুটি এমন চমৎকারভাবে নিজেদের ঢেকে রাখে যে, ওরা যে আলাদা, তা ঠিক ধরাও পড়ে না। বিশেষ করে ছয় কিংবা দশের বৃত্ত ছাড়িয়ে আমরা যখন চোদ্দো মাত্রায় গিয়ে পৌঁছই, অতিরিক্ত ওই দু-মাত্রাকে তখন ছন্দের মূল চালেরই অঙ্গ বলে মনে হয়।” অর্থাৎ চোদ্দ মাত্রার লাইনটা তখন আর ছোটো মাপের বিচার অনুযায়ী ৪+৪+৪+১২ থাকে না, বড়ো মাপের চালে সেটা ৮+৬ হয়ে ওঠে। এটা যেমন অক্ষরবৃত্তের পক্ষে সত্য, তেমনিই ৪-মাত্রার মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্তের পক্ষেও সত্য। যা ছিল ছোটো-ছোটো অংশের সমষ্টি, তা দুটি বড়ো মাপের অংশ হয়ে দাঁড়ায়। এই যে দুই অংশে বিন্যস্ত পঙক্তির আট-ছয় বন্ধ, একেই বলে পয়ার-বন্ধ। এই বন্ধে বাংলায় যেমন সেকালে ও একালে অক্ষরবৃত্তের কবিতা প্রচুর লেখা হয়েছে, তেমনি রবীন্দ্রনাথ নিজে ও তাঁর পরবর্তী কবিরা এই বন্ধে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তেও কম কবিতা লেখেননি।
আসুন, আমরা নিজেরাই এবারে এই বন্ধে দু-লাইন লিখে ফেলি :
নিম্নে আদিগন্ত শুধু / সমুদ্র সুনীল
ঊর্ধ্বাকাশে উড়ে যায় / দুটি গাংচিল
এ হল পয়ারে-বাঁধা অক্ষরবৃত্তের নমুনা। তেমনি–
নীচে আদিগন্ত-যে / সিন্ধু সুনীল
ঊর্ধ্বে মেলেছে ডানা / দুটি গাংচিল
এ হল পয়ারে-বাঁধা মাত্রাবৃত্ত। ঠিক তেমনি—
যোজন-যোজন নীলের খেলা / সমুদ্দুরের জলে
ঊর্ধ্বাকাশে শুভ্র দুটি / সারস উড়ে চলে
এ হল পয়ারে-বাঁধা স্বরবৃত্তের দৃষ্টান্ত। (ছন্দ ঠিক রেখে চটপট ছাড়া বানাতে গিয়ে চিলকে সারস করে দিলুম, তার জন্যে চিলের কাছে তো বটেই, পড়ুয়াদের কাছেও ক্ষমা ভিক্ষা করি।) বলা বাহুল্য, যেহেতু ছন্দটা এখানে স্বরবৃত্ত, তাই সিলেবল-এর হিসেবে এখানে মাত্ৰাসংখ্যা ধরতে হবে।
পয়ার-বন্ধের কথা তো বলা গেল, এবারে খুব সংক্ষেপে মহাপয়ারের কথা বলা যাক। মহাপয়ারের নামেই প্রমাণ, ওটি আর-কিছু নয়, পয়ারেরই একটা বড় সংস্করণ। পয়ার যে-ক্ষেত্রে আট-ছায়ের বন্ধ, মহাপয়ার সে-ক্ষেত্রে আট-দশের। অর্থাৎ মহাপয়ারের বেলায় পঙক্তির প্রথমাংশে – পয়ারের মতোই- আট মাত্রা থাকে, কিন্তু দ্বিতীয়াংশ আরও বড়ো চালে দশ মাত্রায় ছড়িয়ে যায়। দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝানো যাক। পয়ারের বেলায় যে-দৃষ্টান্ত দিয়েছি, তারই বক্তব্যকে এখানে মহাপয়ারে বান্ধব।
নিম্নে সারাদিন দেখি / আদিগন্ত সমুদ্র সুনীল
ঊর্ধ্বে শ্বেতবিন্দুসম / উড়ে যায় দুটি গাংচিল।
এ হল মহাপয়ারে-বাঁধা অক্ষরবৃত্তের নমুনা। আবার—
নীচে আদিগন্ত-যে / চঞল সিন্ধু সুনীল ঊর্ধ্বে মেলেছে ডানা / সুন্দর দুটি গাংচিল এ হল মহাপয়ারে-বাঁধা মাত্রাবৃত্ত। আবার
যোজন-যোজন দেখছি শুধু / নীলের খেলা সমুদুরের জলে
ঊর্ধ্বকাশে পাল্লা দিয়ে / শুভ্র দুটি সারস উড়ে চলে।
এ হল মহাপয়ারে-বাঁধা স্বরবৃত্তের দৃষ্টান্ত। (হায় চিল, ছন্দের খাতিরে আবার তোমাকে সারস বানালুম!)
পয়ারি-মহাপয়ার প্রসঙ্গ এখানেই শেষ হল। এর পরে আসছে পদ, যতি ও যতিলোপের কথা।
০৯. পদ, যতি ও যতিলোপ
এবারে আমরা পদ-প্রসঙ্গে ঢুকব। পদ করে কয়? পিয়ার নিয়ে আলোচনার সময়ে তার কিছুটা আভাস দিয়েছিলুম। এবারে আর-একটু বিস্তারিতভাবে তার সুলুকসন্ধান নেওয়া দরকার।
সনেট তো চোদ্দো পঙক্তির কবিতা। বাংলায় তাকে আমরা চতুৰ্দশপদী কবিতা বলি। সেই বিচারে ‘পদ কথাটার অর্থ দাঁড়ায় পঙক্তি। শব্দকোশেও অন্যান্য অর্থের সঙ্গে, এই অর্থটা দেওয়া আছে বটে। কিন্তু এখানে আমরা ‘পদ” বলতে যা বোঝাতে চাইছি, তাতে এই অর্থটা পরিত্যাজ্য। কেন-না, একটু বাদেই আমরা দেখব যে, কবিতার পঙক্তিতে অনেকসময়ে একাধিক পদ থাকে। সেক্ষেত্রে, ‘পদ” বলতে যদি আমরা ‘পঙক্তি’ বুঝি, তাহলে ‘দ্বিপদী পঙক্তি’ কথাটার অর্থ দাঁড়াবে ‘দ্বি-পঙক্তিক পঙক্তি’, এবং ব্যাপারটা তখন খুবই ধোঁয়াটে হয়ে দাঁড়াবে।
তার চেয়ে বরং ‘পদ” বলতে ‘পদক্ষেপ” বোঝাই ভালো। বস্তৃত, প্রতি পদক্ষেপে যেখানে বিপদের আশঙ্কা কিংবা আনন্দের আশ্বাস রয়েছে, সেখানে তো আমরা ‘পদে-পদে বিপদ’ কিংবা ‘পদে-পদে আনন্দ”-এর কথাই বলে থাকি। (উদাহরণ : “নিবিড় ব্যথার সাথে পদে-পদে পরম সুন্দর”— রবীন্দ্রনাথ।)
এখন ব্যাপার হচ্ছে এই যে, কবিতার পঙক্তিগুলিকে তো আমরা একটানা পড়ে। যাই না, একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাব, আমরা যখন কবিতা পড়ি, তখন সেই কবিতার এক-একটি পঙক্তি একাধিক অংশে বিভক্ত হয়ে যায়। এটা হয় ছন্দের চালের জন্য। তা যেমন অক্ষরবৃত্ত ছন্দ, তেমনই পয়ার-বন্ধের আলোচনার সময়ে আমরা দু-রকম চালের কথা জেনেছিলুম। ছোটো-মাপের চাল আর বড়ো-মাপের চাল। চাল না-বলে একে চলন কিংবা পদক্ষেপও বলতে পারি। সত্যি, এ যেন দু-রকমের পদক্ষেপ। ছোটো-মাপের ও বড়ো-মাপের। এই দুই-মাপের পদক্ষেপ, আসলে, কবিতার পঙক্তির ভিতরকার দুই-মাপের দুটি অংশকে আলাদা করে চিনিয়ে দেয়। আমরা যখন ছোটো পদক্ষেপে চলি, তখন ছোটো-মাপের অংশটাকে ধরতে পারি। আর বড়ো-পদক্ষেপে চললে সন্ধান পাই বড়ো-মাপের অংশের। ছোটো-মাপের অংশকে আমরা বলি। ‘পৰ্ব’’। বড়ো-মাপের অংশকে বলি “পদ”।
পদক্ষেপ-এর কথাটা যখন বলেইছি, তখন আর-একটু বিশদ করে বলা যাক। পদক্ষেপ করতে-করতে এগোনো মানে বারবার পা-ফেলা ও পা-তোলা। এই পাফেলা ও পা-তোলার মধ্যে একটু বিরতি ঘটে। এ যেন চলার মধ্যেই একটু থেমে থাকার ব্যাপার। আমরা যখন কবিতা পড়ি, তখন একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর, প্রায় আমাদের অগোচরে, এই থেমে-থাকার ব্যাপারটা ঘটতে থাকে। আমরা একটু চলি, একটু থামি, একটু চলি, একটু থামি— এই রকমের ব্যাপার। আর কী। কবিতায় এই থেমে-থাকার ব্যাপারটাকেই বলি ‘যতি’।
‘যতি’ আছে তিন রকমের। ছোটো যতি, মাঝারি যতি আর বড়ো যতি। ছান্দসিক এর নাম দিয়েছেন লঘুযাতি, অর্ধর্যাতি আর পূর্ণযতি। কবিতার পঙক্তির মধ্যে পর্ব যেহেতু সবচেয়ে ছোটো অংশ, তাই তার পরে আসে লঘুযতি; আর পদের মাপ যেহেতু পর্বের চেয়ে বড়ো, তাই তার পরে আসে অর্ধযতি।। পঙক্তির মাপ আরও বড়ো। তাই পূৰ্ণযতি আসে পঙক্তির শেষে।
একটা দৃষ্টান্ত দিই।
নতমুখে বলেছিলে, চিত্তে রেখো আশা
আঁধারেও দীপ্তি যেন পায় ভালোবাসা।
এই যে অক্ষরবৃত্ত-ছন্দ-লেখা দুটি পঙক্তি, ছোটো-পদক্ষেপে চললে— ছন্দের চাল অনুযায়ী— এরা পর্বে-পর্বে এইভাবে ভাগ হয়ে যাবে :
নতমুখে/বলেছিলে/চিত্তে রেখো/আশা,
আঁধারেও/দীপ্তি যেন/পায় ভালো/বাসা।
সেক্ষেত্রে প্রতি পর্বের শেষে আমরা একটুক্ষণের জন্য থেমে দাঁড়াব, এবং এই যে একটুক্ষণের জন্য থেমে দাঁড়ানো, এটাই হচ্ছে লঘুযতি।।
বড়ো-পদক্ষেপে চললে কিন্তু পর্বে-পর্বে বিভক্ত না-হয়ে এই পঙক্তি দুটি আর একটু বড়ো-মাপে অর্থাৎ পদে-পদে ভাগ হয়ে যাবে। তখন ভাগটা হবে এইরকম :
নতমুখে বলেছিলে,/চিত্তে রেখো আশা,
আঁধারেও দীপ্তি যেন/পায় ভালোবাসা।
তখন দেখতে পাব যে, দুটি পঙক্তির প্রতিটির মধ্যেই রয়েছে দুটি করে পদ; অর্থাৎ এই পঙক্তি দুটি হচ্ছে দ্বিপদী পঙক্তি। (প্রথম পদ আর্ট-মাত্রার; দ্বিতীয় পদ ছ-মাত্রার) সেইসঙ্গে আর-একটা জিনিসও দেখা যাবে। সেটা এই যে, ছোটো-পদক্ষেপে চললে পর্বশেষে আমরা যেটুকু সময়ের জন্যে থেমে দাঁড়াচ্ছিলুম, বড়ো-পদক্ষেপে চলার ফলে পদশেষে তার চাইতে আর-একটু বেশি সময়ের জন্যে আমাদের থামতে হচ্ছে। আর দ্বিতীয় পদের সঙ্গে-সঙ্গে এক্ষেত্রে যেহেতু পঙক্তির সীমানাও শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাই সেখানে থামতে হচ্ছে আরও-একটু বেশি সময়ের জন্যে। পদশেষে আর পঙক্তি শেষে এই যে থেমে দাঁড়ানো, যথাক্রমে এরাই হচ্ছে অর্ধযাতি আর পূর্ণযতি।
অক্ষরবৃত্তের বদলে এবারে দ্বিপদী এই পঙক্তি দুটিকে আমরা মাত্রাবৃত্তে ঢালাই করব। যদি ৬-মাত্রার মাত্রাবৃত্তে ঢালাই করি, তাহলে এদের চেহারা দাঁড়াবে এইরকম :
নতমুখে তুমি বলেছিলে যেন চিত্তে খানিক আশা
জেগে থাকে। আর আঁধারেও যেন জ্বলে ওঠে ভালোবাসা।
এ-দুটিও দ্বিপদী পঙক্তি। পদে-পদে ভাগ করলে ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়াবে :
নতমুখে তুমি বলেছিলে যেন / চিত্তে খানিক আশা
জেগে থাকে। আর আঁধারেও যেন / জ্বলে ওঠে ভালোবাসা।
পঙক্তি দুটিকে আমরা স্বরবৃত্তেও ঢালাই করতে পারি। লিখতে পারি :
শান্ত গলায় বলেছিলে, চিত্তে রাখো আশা
অন্ধকারের বুকে জ্বালাও গভীর ভালোবাসা।
এ-ও দ্বিপদী পঙক্তি। এর পদবিভক্তি হবে এইরকম :
শান্ত গলায় বলেছিলে / চিত্তে রাখো আশা,
অন্ধকারের বুকে জ্বালাও / গভীর ভালোবাসা।
এবারে ত্রিপদী পঙক্তির দৃষ্টান্ত দিই :
অবশ্যই তার চেয়ে আছে আরও ভাল মেয়ে, কিন্তু হে ঘটক,
আগে তারই কথা কও, অন্যথা বিদায় হও, সম্মুখে ফটক।
এর পদ-বিভাজন হবে এই রকম :
অবশ্যই তার চেয়ে / আছে আরও ভালো মেয়ে/কিন্তু হে ঘটক,
আগে তারই কথা কও,/অন্যথা বিদায় হও,/ সম্মুখে ফটক।
শব্দগুলিকে, ছন্দের চাল অনুযায়ী, এখানে দুই পঙক্তিতে সাজানো হয়েছে। আগেকার দিন হলে অবশ্য অন্য-বিন্যাসে এদের সাজানো হত। বিন্যাসটা হত এই-রকম :
অবশ্যই তার চেয়ে আছে আরও ভালো মেয়ে
কিন্তু হে ঘটক,
আগে তারই কথা কও, অন্যথা বিদায় হও,
সম্মুখে ফটক।
বলা বাহুল্য, ঘটক-মহাশয়ের প্রতি নিবেদিত এই শব্দাবলিকে এখানে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ধরা হয়েছে। সেক্ষেত্রে, মাত্রাবৃত্ত কিংবা স্বরবৃত্তেও একে বিন্যস্ত করা যেত। কিন্তু আমরা তো এখানে ছন্দের পার্থক্য বুঝতে বসিনি, পদ-পরিচয়টাই শুধু পেতে চাইছি। আশা করি, সেই পরিচয় ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়েছে।
এবারে একটু যতির কথায় ফিরব। যতির পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। কিন্তু একটা জরুরি কথা তখন জানা হয়নি। সেটা এই যে, লঘুযতি ও অর্ধার্যতি মাঝে-মাঝে লোপ পেয়ে যায়। অর্থাৎ পর্ব কিংবা পদের শেষে তখন আর থেমে দাঁড়াবার উপায়। থাকে না। পুরোনো সেই উদাহরণটির উপরে আর-এক বার চোখ রাখা যাক :
নতমুখে বলেছিলেন, চিত্তে রেখো আশা,
আঁধারেও দীপ্তি যেন পায় ভালোবাসা।
পর্বের হিসেব করলে দেখা যাবে যে, অক্ষরবৃত্তে-লেখা এই পঙক্তি দুটির প্রতিটিতে আছে তিনটি করে পর্ব ও একটি করে ভাঙা-পর্ব। আবার, পদের হিসেব নিলে দেখতে পাব যে, এই পঙক্তি দুটির প্রতিটিতে আছে দুটি করে পদ। এখন কথা হচ্ছে, পর্ব ও পদের সীমানা এখানে এতই স্পষ্ট যে, পর্বশেষের লঘুযাতি ও পদশেষের অর্ধযতির ব্যাপারটাকে বুঝে নিতে এক্ষেত্রে আমাদের কিছু অসুবিধে হয়নি। কিন্তু আমরা যখন কবিতা লিখি, তখন পর্ব ও পদের সীমানা কি সর্বত্র এমন স্পষ্টভাবে টেনে দেওয়া যায়? যায় না। (পর্বের সীমানা তো মাঝে-মাঝেই অস্পষ্ট থেকে যায়।) কেন? কারণটা আর-কিছুই নয়, পর্ব অথবা পদের সঙ্গে শব্দের বিরোধ। পর্ব অথবা পদের সীমানা শেষ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও যখন শব্দের সীমানা শেষ হয় না, তখন অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় যে, (শব্দটাকে না ভেঙে) গোটা শব্দটাকে একসঙ্গে উচ্চারণ করবার প্রয়োজনে আমরা পর্ব অথবা পদের শেষে থেমে দাঁড়াতে পারছি না। আর তখনই আমরা বুঝতে পারি যে, লঘুযতি ও অর্ধর্যাতি এক্ষেত্রে লোপ পেয়ে গেল।
আগের উদাহরণের সামান্য-কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে এবারে নতুন করে সাজিয়ে নেওয়া যাক। লেখা যাক :
অস্ফুট বলেছ, যেন চিত্তে থাকে আশা,
আঁধারে অম্লান যেন জ্বলে ভালোবাসা।
বলা বাহুল্য, এইভাবে লিখলেও পঙক্তি দুটির ছন্দ একই থাকবে, কিন্তু দুটি পঙক্তির কোনওটিরই প্রথম পর্বের সীমানাকে এক্ষেত্রে আর স্পষ্ট করে দেখানো যাবে না। ফলে প্রথম পর্বের শেষে আর আমরা থেমে দাঁড়াতেও পারব না। পঙক্তি দুটির পর্ব বিভাজন এক্ষেত্রে এইরকম হবে 🙂
অস্ফুট ব : লেছ, যেন / চিত্তে থাকে / আশা,
আঁধারে অ : ম্লান যেন / জ্বলে ভালো / বাসা।
পর্বশেষের লঘুযতি কীভাবে লোপ পায় আমরা তা দেখলুম। এতে ছন্দের কোনও হানি হয় না, বরং তার বিন্যাসে বেশ-একটা বৈচিত্র্যের ছোঁয়া লাগে।
পর্বান্তিক লঘুযতির মতো পদান্তিক অর্ধযতিও অনেকক্ষেত্রে লোপ পায়। কীভাবে পায়, আগের ওই উদারণটিকেই আরও-একটু ঘুরিয়ে সাজালে সেটা বোঝা যাবে। যেমন, ধরা যাক, আমরা যদি লিখি :
নতমুখে বলেছিলেন, হৃদয়ে রেখো আশা,
অন্ধকারে অন্নান জ্বলুক ভালোবাসা।
তাহলে এই পঙক্তি দুটির প্রথম পদ ও দ্বিতীয় পদের মধ্যবর্তী সীমারেখা স্পষ্ট হয়ে ফুটবে কি? ফুটবে না। পদ-বিভাজন সে-ক্ষেত্রে এই রকম হবে :
নতমুখে বলেছ, হু : দয়ে রাখো আশা,
অন্ধকারে অম্লান জ্ব : লুক ভালবাসা।
অর্থাৎ প্রথম পঙক্তির হৃদয়ে ও দ্বিতীয় পঙক্তির ‘জ্বলুক’ শব্দকে না ভেঙে আমরা একটানা উচ্চারণ করতে চাইব (কেন-না, সেটাই স্বাভাবিক উচ্চারণ), এবং তারই ফলে, প্রথম ও দ্বিতীয় পঙক্তির প্রথম পদের শেষে আমরা থেমে দাঁড়াতে পারব না। তখন আমরা বুঝে নেব যে পদান্তিক অর্ধর্ষতি এক্ষেত্রে লোপ পেয়ে গেল।
কিন্তু লঘুযতির বিলোপ যদিও পঙক্তি-বিন্যাসের কোনও ক্ষতি করে না, অর্ধার্যতির বিলোপ তাকে বেশ-খানিকটা ধাক্কা দেয়। কবিতার বিন্যাসে যারা আদ্যন্ত মসৃণতার পক্ষপাতী, তাদের পক্ষে তাই অর্ধার্যতিকে যথাসম্ভব বঁচিয়ে রাখবার চেষ্টা করাই ভালো।
প্রসঙ্গত, একটা কথা বলি। লঘুযতি ও অর্ধার্যতি কীভাবে লোপ পায়, সেটা বোঝাবার জন্য আমরা এখানে যেসব উদাহরণের সাহায্য নিয়েছি, সেগুলি অক্ষরবৃত্তে লেখা। সেক্ষেত্রে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তে লেখা পঙক্তির সাহায্যেও যতিলোপের ব্যাপারটা অবশ্যই বুঝিয়ে বলা যেত। কিন্তু তার আর কোনও দরকার আছে কি? নেই নিশ্চয়?
কবিতার ক্লাসে তাহলে এখানেই আমি ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে দিলুম। এবারে পড়ুয়াদের মধ্যে উপাধিপত্র বিতরণের পালা। এই উপলক্ষে আমি পদ্যে একটি ভাষণ দিতে চাই।
১০. উপাধি-বিতরণ উপলক্ষে কবিকঙ্কণের ভাষণ
কবিতার ক্লাস অদ্য হৈল সমাপন,
কিছু উপদেশ দিব, শূন ছাত্ৰগণ।
বহুবিধ কৰ্ম আছে জগৎসংসারে,
তেমতি কর্মীও আছে হাজারে-হাজারে।
কেহ তেজারিতি করে, কেহ-বা মোক্তারি,
কেহ-বা দালালি করে, কেহ ঠিকাদারি।
কেহ-বা সাজায় যত্নে ইষ্টকের পাঁজা,
কেহ-বা পিষ্টক গড়ে, কেহ তেলেভাজা।
কেহ-বা পড়ায় ছাত্র, বিদ্যালয়ে যায়,
রাস্তার উপরে কেহ বান্দর নাচায়।
কেহ কৃষিকর্ম করে, কেহ ধান ভানে,
কেহ-বা চালায় টেমপে, কেহ রিকশা টানে।
পানের বোটাটি হস্তে, নাহি-ক সময়,
চলেছে দপ্তরে কেহ, ব্যস্ত অতিশয়।
কেহ-বা ডাক্তারি করে, বত্ৰিশ টাকার
ভিজিটে ছত্রিশ-তলা বাড়ি ওঠে তার।
কেহ করে রাজনীতি, অন্যের মাথায়
কৌশলে কঁঠাল ভেঙে মহানন্দে খায়।
কেহ তৈল বেচে, কেহ তেলা মস্তকের
উপরেই তৈল ঢেলে গুছায় আখের।
কেহ করে জনসেবা, ধন্য হয় দেশ;
কেহ-বা কাজের মধ্যে উলটায় গণেশ।
এইমতো নানা লোকে নানা কর্ম করে,
কর্মী নামে খ্যাত হয় বিশ্ব-চরাচরের
কর্মযোগী কৰ্মবীর নানা আখ্যা পায়,
কর্মের জাতাটি তারা অক্লেশে ঘুরায়।
তেমতি কবিতা লেখা কর্ম যদি হয়,
কবিকেও লোকে কমী বলিত নিশ্চয়।
কিন্তু যে কবিতা লেখে,- শিশু বৃদ্ধ নারী
সকলেই বলে তাকে ‘অকর্মর ধাড়ি’।
অশান্তিতে জ্বলে সদা কবির সংসার,
ভাই বন্ধু সকলেই নিন্দা করে তার।
“এইবারে ত্যাজ্যপুত্ৰ করিব ব্যাটাকে।”
জায়াও সর্বদা কয় মুখ করি কালো,
“ইহাপেক্ষা ডাকতের হাতে পড়া ভালো।”
বাড়িওলা শোনে যদি, নূতন ভাড়াটে
পদ্য লেখে, তবে তার ভয়ে দিন কাটে।
ইদানীং মুদিরাও হয়েছে সেয়ানা,
কবিকে বাকিতে তারা কিছুই দেয় না।
অধিক কবি কী, কোনো কাবুলিওলাও
কবিকে দেয় না কার্জ বলে, “ভাগ যাও।”
এইসব ভেবেচিন্তে ছাত্ৰগণ সবে
ঠিক করো, কবি কিংবা কৰ্মবীর হবে।
পিতার ধমক, মুদি যাবদের তাড়া,
বন্ধুদের ব্যঙ্গ, গৃহিণীর মুখনাড়া,
কোনোদিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি নাহি হেনে,
সবকিছু ললাটস্য লিখনং’ জেনে
তবু পদ্য লিখিবার ইচ্ছা যদি হয়
মাঝে-মাঝে দুই ছত্র লিখিবা নিশ্চয়।
নিত্যও লিখিতে পারো, তবে কথা এই,
যত কবি বঙ্গে, তত পাঠক তো নেই।
আর যদি পাঠকের না করো পরোয়া,
তাহলে উত্তম কথা, সে তো বারো পোয়া।
সকালে লিখিয়ো তবে, দুপুরে লিখিয়ো,
বিকালে লিখিয়ো, শুধু রাত্রে ঘুম দিয়ে।
লিখিবার অন্ধিসন্ধি জেনেছ সবাই,
কবিতার ক্লাসে, তাই চিন্তা আর নাই।
শিখছ ছন্দের রীতি, বাক্যের কায়দা,
এইবারে তাহাতেই উঠিবে ফায়দা।
স্নাতক-উপাধি আমি দিলাম সকলে।
(জানি না কী ধুধুমার হবে তার ফলে।)
কবিকঙ্কণের কথা শেষ হৈল, আর
কথা নাই কিছু, যাও, সকলে এবার
তত পদ্য লেখো বাছা, যত ইচ্ছা হয়,
শুধু এক অনুরোধ, রাখিবা নিশ্চয়।
দৈনিক কাগজে পদ্য নাহি যায় ছাপা—
নিতান্ত সহজ কথা, মনে রেখে বাপা।
সুতরাং লেখো পদ্য হাজারে হাজারে,
কিন্তু তাহা পাঠিয়ো না ‘আনন্দবাজারে’।
সংযোজন ১ : গৈরিশ ছন্দ
গিরিশচন্দ্র যেসব নাটক লিখেছিলেন, তার সবই যে ছন্দোবদ্ধ, তা নয়। যেসমস্ত নাটক পৌরাণিক আখ্যানের ভিত্তিতে লেখা, কিংবা গোত্ৰবিচারে যা রোমান্টিক, শুধু তারই সংলাপকে তিনি ছন্দে বেঁধেছিলেন। আবার সেখানেও যে তার সমস্ত চরিত্রের সংলাপ একই ছন্দে বাঁধা, তা-ও নয়। একাধিক রকমের ছন্দের দোলা সেখানে আমরা দেখতে পাই। তার মধ্যে যেটা প্রধান ছন্দ, তাকেই আমরা ‘গৈরিশ ছন্দ’ বলে থাকি। একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :
“অভেদ কোরো না ভেদ, সতি!
জেনো মাতা,
ভাগীরথী-পাৰ্বতী, অভেদ।
বামদেব বাম
ভাবিলে, মা, অন্তর শিহরে!
কুমার আবদ্ধ বুঝি ভৈরবী মায়ায়!
বাক্য ধরো, অনুরোধ রক্ষা করো, মাতা।
শিবরানি সদয়া না-হলে
রুষ্ট শিব তুষ্ট নাহি হবে…।”
গিরিশচন্দ্রের জনা নাটক থেকে অগ্নির সংলাপের একটা অংশ এখানে তুলে দিলুম। যে-ছন্দে এই সংলাপ বাঁধা, তাকে একটা আলাদা রকমের ছন্দ বলে ভাবতে আমরা অভ্যস্ত হয়েছি। কী ছন্দ? না, গৈরিশ ছন্দ।
কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, গৈরিশ ছন্দ কি সত্যিই একটা আলাদা রকমের ছন্দ? তা কিন্তু নয়। পয়ার যেমন আলাদা কোনও ছন্দ নয়, ত্ৰিবিধ ছন্দের একটা বিশেষ রকমের বঁধনমাত্র, গৈরিশ ছন্দও আসলে তা-ই। মূল ছন্দ এখানে অক্ষরবৃত্ত বা মিশ্রকলাবৃত্ত। গিরিশচন্দ্ৰ সেই মূল ছন্দকে একটা বিশেষ বাঁধনে বেঁধেছিলেন, এবং সেই বাঁধন বা বিন্যাসটাই গৈরিশ ছন্দ বলে প্রসিদ্ধি পেয়েছে।
লক্ষণীয় যে, অক্ষরবৃত্ত এখানে অমিল বা অমিত্ৰাক্ষর। পঙক্তিশেষে মিল রাখবার ব্যবসথা। এখানে নেই। কিন্তু সেটাও কোনও নতুন ব্যাপার নয়। এমনকি, নাটকরচনার ক্ষেত্রেও নয়। একথা এইজন্যে বলছি যে, মাইকেল মধুসূদনের পদ্মাবতী নাটকের বেশ-কিছু সংলাপ ইতিপূর্বে এই অমিল অক্ষরবৃত্তেই রচিত হয়েছিল। নাটকের সংলাপে ব্যবহৃত ছন্দের ব্যাপারে গিরিশচন্দ্ৰকে, অন্তত সেই বিচারে, কোনও নতুন পথের স্রষ্টা আমরা বলতে পারি না। পথিকৃৎ এক্ষেত্রে গিরিশচন্দ্ৰ নন, মাইকেল।
তবে কি গিরিশচন্দ্ৰ এক্ষেত্রে মাইকেলের অনুসারীমাত্র? না, তা নয়। মাইকেলের হাতে যার প্রবর্তন, সেই অমিল অক্ষরবৃত্তের বিন্যাসে একটা মস্ত পরিবর্তন তিনি ঘটিয়ে দিয়েছিলেন। মাইকেলের সঙ্গে এ-ব্যাপারে তার পার্থক্যটা এইখানে যে, গিরিশচন্দ্ৰ তীর অক্ষরবৃত্তে-রচিত সংলাপের পঙক্তিগুলিকে একই মাপের রাখেননি; পঙক্তি থেকে ভাঙা পর্বকে ইচ্ছেমতো বাদ দিয়েছেন; তা ছাড়া, যত্রতত্র যতির ব্যবস্থা না-করে এমনভাবে তার যতিগুলিকে তিনি বিন্যস্ত করেছেন, যাতে সংলাপটািকে ঠিকমতো বলে যাবার ব্যাপারে কারও কোনও অসুবিধে না হয়। যতির এই স্বাভাবিক বিন্যাসের ফলে গিরিশচন্দ্রের নাট্যসংলাপে যে একটা অবাধ গতির সঞার হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।
যা-ই হোক, আসল কথাটা হচ্ছে এই যে, আমরা যাকে গৈরিশ ছন্দ বলি, বস্তৃত তাকে অমিল অক্ষরবৃত্তের গৈরিশ বিন্যাস বললেই ঠিক হয়। এই বিন্যাসই জানিয়ে দেয় যে,অক্ষরবৃত্তের ব্যবহারে গিরিশচন্দ্রের দক্ষতা ছিল উল্লেখযোগ্য। আবার, ওই জনা নাটকেই বসন্তকে যখন আমরা বলতে শুনি :
“ওলো তোর নিত্যি নূতন ঢং,
বালাই বালাই, ছাই মুখে তোর, এ কী আবার রং!
এমন কথা বলবি যদি আর,
চলে যাব তোর সোহাগের মুখে দিয়ে ক্ষার…।”
তখন আমরা বুঝতে পারি যে, স্বরবৃত্ত বা দলবৃত্তের ব্যবহারেও তাঁর দক্ষতা কিছু কম ছিল না।
অবশ্য আমরা সবচেয়ে বিস্মিত হই। তখন, যখন দেখি যে, কোনও রকমের কাব্যছন্দের দোলাই যার মধ্যে নেই, সাদামাঠা গদ্যে রচিত সেই সংলাপের মধ্যেও অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে কিছু মিল তিনি ঢুকিয়ে দিয়েছেন। ওই জনা নাটকের বিদূষক যখন বলে, “হরি হে, তোমার দোহাই- শীঘ্র না চরণ পাই। দুটো মোন্ডা খেতে এসেছি। দু-দিন, খেয়ে যাই।” তখন গোপন সেই মিলগুলি যে গদ্যের মধ্যেও খানিকটা দোল লাগায়, এবং তাকে – অন্তত খানিকটা পরিমাণে- পদ্যের দিকে এগিয়ে দেয়, তা-ও স্বীকার্য। সত্যি বলতে কী, গদ্যে-পদ্যে এই যে মেলবন্ধন তিনি ঘটিয়েছিলেন, যার ছায়া অত্যন্ত আধুনিক কালের কবিতার শরীরেও আমরা দেখতে পাই, এরই তাৎপর্য হয়তো সবচেয়ে বেশি।
১২. সংযোজন ২; ছন্দের সহজপাঠ
মজাটা নেহাত মন্দ নয়। কবিতা কেমন লেখা হচ্ছে, তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠছে। না, তার বদলে প্রশ্ন উঠছে কবিরা ছন্দ জানেন কি জানেন না, তাই নিয়ে। অর্থাৎ একেবারে শিকড় ধরে টান মারা হচ্ছে। কেউ-কেউ তো দেখছি প্রশ্ন তোলারও ধারা ধারছেন না, অম্লানবদনে বলে দিচ্ছেন যে, একালে যারা কবিতা লিখছেন, ছন্দের একেবারে প্রাথমিক পাঠও তারা নেননি। সাদা বাংলায়, ছন্দ নামক ব্যাপারটার ‘হ-ক্ষ’ তো দূরের কথা, ‘অ-আ-ক-খও তাদের জানা নেই। তবু যদি তারা ওইসব ছাইপাশ লিখতে চান তো লিখুন, কিন্তু সম্পাদকমশাইরা সাবধান, ‘কবিতা’ নাম দিয়ে ওই ব্যভিচারগুলিকে আর ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করবেন না।
শুনে কার কী মনে হয় জানি না, এই লেখকের কিন্তু পাগলা মেহের আলির কথাটাই বারবার মনে পড়ে যায়। “তফাত যাও, তফাত যাও। সব ঝুট্ হ্যায়, সব ঝুঁট্ হ্যায়।”
তবে কিনা বাংলা কবিতা সম্পর্কে (এবং, বলা বাহুল্য, কবিদের সম্পর্কেও) এমন মন্তব্য যে এই প্রথম শোনা গেল, তা-ও নয়। মোটামুটি এই একই ধরনের কথা শুনছি। অনেক বছর ধরেই। অনেক বছর মানে কত বছর? তা পঞিাশ বছর তো হবেই, কিছু বেশিও হতে পারে। কাদের সম্পর্কে এবং কোন কবিতা সম্পর্কে এমন মন্তব্য? দয়া করে তাহলে শুনুন।
যখন ইস্কুলে পড়ি, তখন রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা- যাতে অন্ত্যমিল ছিল না। বটে, কিন্তু মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দের বাঁধুনি ছিল একেবারে টানটান, উপরন্তু আঠারোমাত্রার পঙক্তিগুলি ছিল একেবারে সমান মাপে টানা- সম্পর্কে এক প্রবীণ পাঠককে বলতে শুনেছিলুম, “দূর দূর, এ আবার কী কবিতা! ছন্দ নেই!” এবারে বলি, প্রাস্তিক-এর এটি প্রথম কবিতা, সেই যার প্রথম পঙক্তিটি হল : “বিশ্বের আলোকলুপ্ত তিমিরের অন্তরালে এল।..”। বলা বাহুল্য, প্রথম কবিতার পরে আর সেই পাঠক এক পা-ও এগোননি। ভালোই করেছিলেন। কেন-না, নিজেরই অর্ধশিক্ষার (যা কিনা অশিক্ষার চেয়েও ভয়ংকর ব্যাপার) কারণে তিনি যাকে ছন্দ বলে চিনেছিলেন, ও-বইয়ের বেশির ভাগ কবিতাতেই তার কোনও সন্ধান তিনি পেতেন না।
যখন কলেজে পড়ি, তখন আবার এই একই অভিযোগ শোনা গেল জীবনানন্দের বিরুদ্ধে। কি না তাঁর ছন্দজ্ঞান বড়ো কম! অভিযোগের সমর্থনে তাঁর যে কবিতাটির সেদিন উল্লেখ করা হয়েছিল, সেটিতেও ছিল না পৌনঃপুনিক অন্ত্যমিলের আয়োজন; তবে প্রতিটি পঙক্তি সমান দৈর্ঘ্যের না হলেও এবং পঙক্তিশেষের ভাঙা-পর্বটি মাঝে-মাঝে বর্জিত হলেও (যা কিনা। রবীন্দ্রনাথও মাঝে-মাঝে অনাবশ্যক বিবেচনায় বর্জন করতেন) ছন্দ ছিল। অবশ্যই। সে-ও পরিপটি মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দ, বিষগ্নতা আর দীর্ঘনিশ্বাস-বিজড়িত বেদনার ভার যা বড়ো সহজে বহন করে। এবারে তবে কবিতাটির নাম বলা যাক। বিখ্যাত কবিতা। ধূসর পাণ্ডুলিপি-র ‘ক্যাম্পে’।
অভিযোগ কি বুদ্ধদেব বসুর বিরুদ্ধেই উঠত না? তা-ও উঠত বইকি। শুধুই যে তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণিত হত কিছু শুচিবায়ুগ্রস্ত মানুষের আপত্তির কোলাহল, তা নয়, বিস্তর পণ্ডিতস্মান্য ব্যক্তির মুখে তখন নিন্দামন্দ শোনা যেত তার ছন্দোজ্ঞানহীনতা’ সম্পর্কেও। এবং নিন্দামন্দ যে অকারণ নয়, তার প্রমাণ হিসেবে তাঁরা উল্লেখ করতেন বন্দীর বন্দনা-র অন্তর্ভুত এমন-সব কবিতার, যাতে ছন্দ ছিল আদ্যন্ত অতি পরিপটি ও সুশৃঙ্খল; না থাকবার মধ্যে শুধ ওই অন্তামিলটাই ছিল না।
চল্লিশের দশকে যাঁরা হরেক পত্রিকায় কবিতা লিখতে শুরু করেন, এক-আধ জনের কথা বাদ দিলে দেখা যাবে যে, আক্রমণের লক্ষ্য এক-কালে তারাও কিছু কম হননি। পরে গালাগাল খেয়েছেন তারাও, যাঁরা কিনা। “পঞ্চাশের কবি” হিসেবে আখ্যাত। এখন আবার গালমন্দ শুনতে হচ্ছে তাদের পরবর্তী কালের কবিদেরও। প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেই একই একঘেয়ে অভিযোগ : ছন্দের ছাঁও এরা জানে না। সুতরাং কবিতা লেখার চেষ্টায় ক্ষান্তি দিয়ে এবারে “তফাত যাও…তফাত যাও”! এই যে অভিযোগ, এর উত্তরে আত্মপক্ষ সমর্থনের মতো হাস্যকর ব্যাপার। আর কিছুই হয় না। চল্লিশের সমর্থনে তাই অন্তত এই লেখকের পক্ষে একেবারে নীরব থাকাই ভালো। তবে পঞ্চাশের কবিরা যে ছন্দ-টন্দের ব্যাপারে একেবারে আকাট রকমের অজ্ঞ ছিলেন, এবং- সেই অজ্ঞতাকে কথার কম্বলে ঢেকেঢুকে রেখেস্রেফ নতুন রকমের উচ্চারণের জোরেই আবার মোড় ঘুরিয়েছিলেন বাংলা কবিতার, এইটে মেনে নেওয়া ভারী শক্ত। যদি বলি যে, তাদের পরে যাঁরা কবিতা লিখেছেন এবং এখনও লিখছেন, ছন্দজ্ঞান তাদেরও মোটামুটি টনটনে, তো মোটেই বাড়িয়ে বলা হবে না।
এরা ছন্দ জানেন না, এমন অভিযোগ তাহলে উঠছে কেন? উঠছে- যদ্দুর বুঝতে পারি— এই জন্য যে, অভিযোস্তাদের নিজেদেরই নেই ছন্দ বিষয়ে কোনও স্পষ্ট ধারণা। ছন্দ বলতে যে ঠিক কী বোঝায়, তা তাঁরা নিজেরাই জানেন না, যদিও তার জন্যে যে সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে র্তাদের কিছু আটকেছে, তা নয়। আটকায়নি। আসলে কোনও কালেই!
বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে আর-একটু খুলে বলি।
প্রান্তিক-এর প্রথম কবিতা পড়ে যিনি বলেছিলেন যে, ওতে ছন্দই নেই’, অনেক বছর পরে তাকে একদিন জিজ্ঞেস করি যে, ছন্দ তো ছিল, তাহলে কেন আমন কথা মনে হল তার। উত্তরে তিনি যে-যুক্তি দিলেন, তাতে তো আমি হতবাক। বন্দীর বন্দনা-র একাধিক কবিতার সূত্রে যাঁরা বলতেন যে, লেখকের ছন্দ-জ্ঞান বড়োই অল্প, তা একরকম “নেই বললেই চলে, একদা হতবাক হয়েছি তাদের কথা শূনেও। মনে-মনে ভেবেছি, ‘ও হরি, এই তাহলে ব্যাপার!”
এখন বিস্ময়বোধ অনেক কমে গিয়েছে। উদ্ভটসাগরদেরই তো এখন আধিপত্য, তাই এসব ব্যাপারে যিনি যতই উদ্ভট কথা বলুন, তাতে আর বিশেষ অবাক হই না। আর তা ছাড়া এই সহজ সত্যটা তো তখনই আমি জেনে গিয়েছি যে, অন্তমিলকেই অনেকে ছন্দ বলে মনে করেন। হালে আবার জানা গেল যে, তাদের সংখ্যাই দিনে দিনে বাড়ছে। পঙক্তি-শেষে চালাক-চালাক মিল থাকলে তবেই সেটা ছন্দ, নইলে নয়। ফলে, যে-কবিতায় অন্ত্যমিলের সাড়ম্বর আয়োজন নেই, তাতেও যে ছন্দ থাকতে পারে, থাকে, এই কথাটা তাদের কিছুতেই বোঝানো যাবে না। ”
তা-ও হয়তো যেত, যদি তারা ছন্দের ব্যাপারে একেবারে কিছুই না জানতেন। সেক্ষেত্রে তারা যে আর-একরকম জেনে বসে আছেন, এবং তারই জোরে জারি করছেন হরেকরকম ফতোয়া, সে-ই হয়েছে মস্ত বিপদ। এখন এই উলটো অ-আ-ক-খ’ তাদের কে ভোলাবে?
ভোলাবার দরকারটাই-বা কী। কিছু না-বুঝে কিংবা বেবাক ভুল বুঝে ছন্দ নিয়ে যাঁর যা খুশি বলুন না, তাতে কান না-দিলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।
এই পর্যন্ত পড়বার পরে অনেকের সন্দেহ হতে পারে যে, এই নিবন্ধের লেখক বোধ হয় অন্ত্যমিল নামক ব্যাপারটারই ঘোর বিরোধী। তা কিন্তু নয়। আসলে, রাইম বা অন্তমিল যে রিদম বা ছন্দের একটা জরুরি শর্ত, এই হাস্যকর কথাটাই সে বিশ্বাস করে না। কেন-না, তা যদি সে বিশ্বাস করত, তাহলে একইসঙ্গে তাকে এটাও বিশ্বাস করতে হত যে, গোটা সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের কোথাও কোনও ছন্দ নেই। না, ছন্দ আর মিল একেবারেই আলাদা দুটো ব্যাপার, পরস্পরের সঙ্গে কোনও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কসূত্রে তারা আবদ্ধ নয়। যা ছন্দোবদ্ধ, তাতে অন্তমিলের ব্যবস্থা অবশ্য থাকতেই পারে, কিন্তু সেটা যে থাকতেই হবে, এমন কোনও কথা নেই। ছন্দ আসলে অনেক বড়ো মাপের ব্যাপার। এতই বড়ো যে, দলবৃত্ত কলাবৃত্ত আর মিশ্রকলাবৃত্ত নামে যে-তিনটি বাংলা ছন্দের পরিচয় আমরা সকলেই রাখি, এবং মোটামুটি যার মধ্যেই দীর্ঘকাল যাবৎ আটকে ছিল বাংলা কবিতা, তার বলয়েও ছন্দ নামক ব্যাপারটাকে সর্বাংশে আঁটানো যাচ্ছে না। তার শরীরের অনেকটাই থেকে যাচ্ছে সেই বলয়ের বাইরে। ফলে, দলবৃত্ত কলাবৃত্ত আর মিশ্রকলাবৃত্ত ছন্দের (এবং তাদের ত্ৰিবিধ নিয়মেরই অন্তর্গত অসংখ্যরকম প্যাটার্ন বা বন্ধের) ধারও ধারছেন না যেসব কবি, এবং সেটা ধারবেন না বলেই এই তিন ছন্দের বলয়ের বাইরে দাঁড়িয়ে লিখছেন তাদের কবিতা (যেমন ধরা যাক, সমর সেন তার সংক্ষিপ্ত কবি-জীবনের আদ্যন্ত লিখেছেন বা অরুণ মিত্র আজও লিখে যাচ্ছেন), তাঁদেরই বা আমরা কোন কানুনে ছন্দোজ্ঞানহীন বলব? কিংবা তাঁদের রচনাকে বলব ছন্দছুট?
যে-কানুনেই বলি না কেন, সেই একই কানুনে তবে তো (শুধু ‘আফ্রিকা’ কি ‘পৃথিবী’ বলে কথা নেই)। রবীন্দ্রনাথের তাবৎ গদ্যকবিতাকেই ছন্দছুট বলতে হয়। রক্ষা এই যে, ‘ছন্দ-টন্দ বোঝে না’ বলে নবীন কবিদের উপরে যাঁরা এখন ছড়ি ঘোরাচ্ছেন, অতটা সাহস তাদের হবে না।
গদ্যকবিতার কথা যখন উঠলই, তখন এই নিয়ে যে-রাসের কথাটা এককালে খুব শোনা যেত, সেটাও বলি। অনেককেই তখন বলতে শুনেছি যে, টানা এক পাতা গদ্য লিখে তারপর ইরেজার দিয়ে তার দু-পাশটা একটু এলোমেলোভাবে মুছে দিলেই সেটা আমনি গদ্যকবিতা হয়ে যায়। খুবই যে মোটাদাগের রসিকতা, তাতে সন্দেহ নেই। যাঁরা বলতেন, তাঁদের সঙ্গে তর্ক করতেও বুচিতে বাধত বলেই আমার এক বন্ধু এই মন্তব্য শুনে একটুও না হেসে খুব অবাক হবার ভান করে। বলতেন, “মুছতে যে হবেই, এমন কথা কে বলল। আপনি দেখছি কিছুই জানেন না। না-মুছলেও কবিতা হয়।” বাজে রসিকতার এটাই ছিল মোক্ষম জবাব।
তখন অন্তত তা-ই ভাবতুম। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে ততই দেখছি, গদ্যের দুপাশ না-মুছলেও যে কবিতা হয়, এর চেয়ে সত্য উক্তি আর কিছুই হতে পারে না। কথাটা হয়তো আগেও কখনও বলেছি, তবু আবার বললেও ক্ষতি নেই যে, কবিতা তো আর-কিছুই নয়, শব্দকে ব্যবহার করবার এক রকমের গুণাপনা, ভাষার মধ্যে যা কিনা অন্যবিধ একটি দ্যোতনা এনে দেয়। সেই দ্যোতনা কি নেহাতই চলতি-অর্থে ছন্দোবদ্ধ রচনার মধ্যে লভ্য? তা ছাড়া, কি তার বাইরে, কোথাও নয়?
এই যে প্রশ্ন, এর কোনও উত্তর আমরা দেব না। শুধু নীচের কয়েকটি লাইন, যা নিশ্চয় সকলেই একাধিকবার পড়েছেন, আরও একবার পড়তে বলব।
“তখন প্ৰলয়কাল, তখন আকাশ্নে তারার আলো ছিল না এবং পৃথিবীর সমস্ত প্ৰদীপ নিবিয়া গেছে- তখন একটা কথা বলিলেও ক্ষতি ছিল। না— কিন্তু একটা কথাও বলা গেল না। কেহ কহাকেও একটা কুশলপ্রশ্নও করিল না।
“কেবল দুইজনে অন্ধরের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পদতলে গাঢ়কৃষ্ণ উন্মত্ত মৃত্যুম্রোত গর্জন করিয়া ছুটিতে লাগিল।”
এবং আরও কয়েকটি লাইন :
“কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী। অন্ধকার রাত্রি। পাখি ডাকিতেছে না। পুষ্করিণীর ধারের নিচ্গাছটি কালো চিত্রপটের উপরে গাঢ়তর কালির প্রলেপের মতো লেপিয়া গেছে। কেবল দক্ষিণের বাতাস এই অন্ধকারে অন্ধভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যেন তাহাকে নিশ্চিতে পাইয়াছে।”
বলা বাহুল্য, প্রচলিত অর্থে ছন্দোবদ্ধ (উপরন্তু সমিল) যে-রচনারীতিকে দীর্ঘদিনের সংস্কারের কারণে অনেকেই একেবারে একমেবাদ্বিতীয়ম কাব্যরীতি বলে ভাবতে অভ্যস্ত, উদ্ধৃত পঙক্তিগুলিকে সেই রীতির সঙ্গে কোনও সম্পর্কসূত্ৰে গাঁথা যাবে না। এমনকি কোনও গদ্যকবিতা থেকেও তুলে আনা হয়নি এই পঙক্তিগুলিকে! তোলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের দুটি গল্প থেকে, যার একটির নাম ‘একরাত্রি’, অন্যটির নাম ‘ত্যাগ’।
অথচ ওই যে দ্যোতনার কথা বলেছি আমরা, ভাষার মধ্যে একমাত্ৰ কবিতাই যার উন্মেষ ঘটায়, এই গদ্যরচনার মধ্যেও তা দেখছি অলভ্য নয়। আর ছন্দ? প্রচলিত তিন বাংলা ছন্দের কথা তাহলে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে ভুলতে হবে আমাদের, সরিয়ে রাখতে হবে ছন্দের ব্যাকরণ থেকে লব্ধ নানা শুকনো সংস্কার, এবং একেবারে গোড়ায় গিয়ে ভাবতে হবে যে, শব্দাবলির যে-পারস্পরিক সংগতি আর সর্বাঙ্গীণ ভারসাম্যের উপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদের ছন্দ-বিষয়ক ধারণা, তারই কি কোনও অনটন এখানে আমাদের চোখে পড়ছে? কই, তা-ও তো পড়ছে कों!
সঞ্চয়িতা থেকে গল্পগুচ্ছ-এ সরে এসেছি। এবারে তবে আরও অনেকটা সরে আসা যাক। ঢুকে পড়া যাক সহজপাঠ প্ৰথম ভাগের মধ্যে।
স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে শিশুদের প্রথম পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হবার ঠিক পরে-পরেই তাদের জন্য ছ-টি বাক্য সেখানে রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বাক্যগুলি এখানে তুলে দিচ্ছি :
বনে থাকে বাঘ।
গাছে থাকে পাখি।
জলে থাকে মাছ।
ডালে আছে। ফল।
পাখি ফল খায়।
পাখা মেলে ওড়ে।
কল্পনাপ্রবণ যে-কোনও শিশুর আগ্রহকে তার ঘরের কোণ থেকে বাইরের পৃথিবীর দিকে- অরণ্য জলাশয় আর আকাশের দিকে- ঘুরিয়ে দিচ্ছে এই ছোটো-ছোটো কয়েকটি বাক্য, যার অনুরণন আমাদের মতো বয়স্ক পাঠকের চিত্তেও চট করে ফুরিয়ে যায় না। একটু ভাবলেই আমরা বুঝতে পারব যে, বক্তব্যের ধারাবাহিক শৃঙ্খলা, শব্দগত সংগতি আর সর্বাঙ্গীণ ভারসাম্য এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের সূত্রে এই বাক্য-কটিকে বেঁধে রেখেছে, আর একই সঙ্গে জাগিয়ে তুলছে সেই আভ্যন্তর আন্দোলন, যাকে খুব সহজেই আমরা ছন্দ বলে শনাক্ত করতে পারি। ধীরে-ধীরে যখন পড়ি, তখন হয়তো সেই ছন্দ ততটা স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে না। কিন্তু তা না-ই পড়ুক, এবং কবিতা হিসাবে না-ই উপস্থাপিত হয়ে থাকুক। এই বাক্যসমষ্টি, মাত্ৰই আঠারোটি শব্দের— এবং খুবই সহজ সরল শব্দের— এই সমাহারও যে বস্তৃত কবিতা-ই, তা-ও তো কারও না বুঝবার কথা নয়।
অনেকই অবশ্য বোঝে না! জানে না যে, গদ্যভাষার মধ্যেও অনেক সময়ে প্রচ্ছন্ন থাকে ছন্দ, যা সেই ভাষার মধ্যে এনে দেয় এক অন্যতর অর্থের দ্যোতনা, এবং সেই দ্যোতনাই তখন গদ্যকে তুলে আনে কবিতার পর্যায়ে।
এখন যাঁরা কবিতা লিখছেন, তাঁদের অনেকেই মনে হয় প্রচলিত তিন ছন্দের কাঠামোর মধ্যে আর আটকে রাখতে চাইছেন না নিজেদের, কবিতার মুক্তি চাইছেন তার বলয়ের বাইরে, সেখানে খুঁজে নিতে চাইছেন অন্যতর ছন্দ। এই যে অন্বেষণ, এর কি কোনও তাৎপর্য নেই? আছে নিশ্চয়। চলতি ছন্দেই যদি সমস্ত কাজ চলত, তবে তো আর কথাই ছিল না। রবীন্দ্রনাথকে তবে আর অত কষ্ট করে মেলে ধরতে হত না কলাবৃত্তের তাবৎ সম্ভাবনার পাপড়িগুলিকে, এবং তারও পরে গিয়ে ঘা দিতে হত না গদ্যকবিতার দরজায়।
অন্বেষণের দরকার অতএব আছেই। কিন্তু কেউ-কেউ সেটা স্বীকার করতে চাইছেন না। এই বলে চেচিয়ে মরছেন যে, ছন্দের একেবারে প্রাথমিক শিক্ষাই এদের হয়নি।
কিছুদিন আগে প্রশ্ন উঠেছিল; এত কবি কেন? পালটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়: তাতে এত গাত্রদাহাঁই-বা কেন? বলতে ইচ্ছে হয় : গোল কোরো না বাবার, যাঁরা লিখছেন, তাদের লিখতে দাও। তবু যদি ঝামেলা করো, তো তোমাদের হাতে এবারে একখানা করে সহজ পাঠ ধরিয়ে দেব।
১৩. পরিশিষ্ট
জিজ্ঞাসু পড়ুয়ার চিঠি – ১
রবিবার দুপুরবেলা। মফসসলের শহরতলিতে সকালবেলায় খবরের কাগজ পাবার উপায় নেই। শরীরটাও বিশেষ ভালো নেই। তাই শুয়ে-শুয়ে খবরের কাগজের পাতা ওলটাতে-ওলটাতে ‘মোহনবাগানের অপরাজিত আখ্যা’ চোখে পড়তেই শরীরটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। খেলার খবর শেষ করেই আবার শরীর এলিয়ে দিলাম। আলস্যবশে পাতা ওলটাতে ওলটাতে চোখে পড়ল কবিতার ক্লাস। আগেও চোখে পড়েছে। কিন্তু কোনও দিন ওই ক্লাসে পাঠ নিতে উৎসাহ হয়নি। আমাদের প্রধান অধ্যাপক মহাশয় বাংলা কবিতা পড়ান। তার কাছে পাঠ নিতে-নিতে কবিতার ক্লাসের প্রতি আমার কেমন একটা অ্যালার্জি হয়ে গেছে। তার ক্লাসে পাঠ নিতে গেলেই গায়ে যেন জুর এসে যায়। তাই আনন্দবাজাক-এর কবিতার ক্লাসের চৌকাঠ মাড়াবার ইচ্ছাও হয়নি কোনও দিন। কিন্তু আজকের অলস দুপুরে ওদিকে তাকাতেই চোখে পড়ে গেল। কয়েকটি ছড়া। ছড়ার টানেই ঢুকে পড়লাম ক্লাসে। ভারী আশ্চর্য লাগল। এ তো কবিকঙ্কণের ক্লাস নয়, স্বয়ং ছন্দ-সরস্বতীর ক্লাস। মনে হল, কবি সত্যেন্দ্রনাথ যে ছন্দ-সরস্বতীর কাছে পাঠ নিয়েছিলেন, আমিও যেন তার কাছেই পাঠ নিচ্ছি। এ হল কী? আমার ছন্দাতঙ্ক রোগটা সেরে গেল কী করে? এই রোগটার একটু ইতিহাস আছে। আমাদের অধ্যাপক মশাই নিজে কবি, তার উপরে গুরুতরভাবে ছন্দ-ভক্ত। আমি বলি, ছন্দের অন্ধভক্ত। তিনি যখন কবিতা পড়েন, তখন কবিতা পড়েন না ছন্দ পড়েন, বোঝা ভার। পড়ানোও তথৈবচ। তার বাইবেল হচ্ছে প্ৰবোধ সেনের ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ বইখানি। আমি বলি, বাইবেল নয়, ছন্দোগ্য উপনিষদ। তাঁর টিউটোরিয়াল ক্লাসের জ্বালায় বইটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হয়েছে। বইটার গুরুত্ব অস্বীকার করবার উপায় নেই। নাড়াচাড়া করবার পক্ষে রীতিমতো গুরুভার। দুৰ্বহ বা দুঃসহ বললেই ঠিক হয়। তাঁর এই বইটা পড়বার চেষ্টা করতে গিয়ে ডি.এল. রায়ের একটি হাসির গান মনে পড়ে গেল। আমনি ওটাকে একটু বদলে নিয়ে দাঁড় করালাম। এই চারটি লাইন :
প্ৰবোধচন্দ্র ছিলেন একটি
ছন্দশাস্ত্ৰ-গ্ৰন্থকার;
এমনি তিনি ছন্দতত্ত্বের
করতেন মর্ম ব্যক্ত–
দিনের মতো জিনিস হত
রাতের মতো অন্ধকার,
জলের মতো বিষয় হত
ইটের মতো শক্ত।
এতেও মনের ঝাল মিটাল না। গ্রন্থকার-অন্ধকার মিলটাও জুতসই নয়। তাই প্রথম লাইনটাকে আরও বদলে দিলাম–
প্ৰবোধচন্দ্র ছিলেন একটি
অপখ্যাত ছন্দকার।
এবার অপখ্যাত আখ্যা দিয়ে মনের ঝালাও মিটাল, ছন্দকার-অন্ধকার মিলে কানও খুশি হল।
প্ৰবোধচন্দ্রের বইটার আরও একটা বিশেষত্ব আছে। এই বইতে রবীন্দ্রনাথের ও অন্যান্য কবিতের ভালো-ভালো কবিতাকে ছন্দের ছুরি দিয়ে এমন কাটাছেঁড়া করা হয়েছে যে, এই বই পড়ার পরে কবিতার উপরেই অশ্রদ্ধা জন্মে যায়। কোনও কোনও বন্ধু এই বইটাকে বলেন কবিতার ডিসেকশান রুম বা পোস্ট মরটেম রুম। আমি বলি কসাইখানা। ভালো-ভালো কবিতার উপরে এরকম নৃশংস উৎপাত দেখে প্ৰবোধ সেন সম্বন্ধেই একটা ছড়া বানিয়েছি। কবিতা-ক্লাসের অন্যান্য পড়ুয়াদেরও যদি আমার মতো। এ-বই পড়বার দুর্ভাগ্য হয়ে থাকে, তবে আমার ছড়াটা শুনে তাঁরাও কিছু সান্ত্বনা পেতে পারেন। তাঁদের তৃপ্তির জন্য ছড়াটা নিবেদন করলাম :
পাকা ধানে মই দেন, ক্ষেত্ৰ চাষেন।
বাংলা কাব্যক্ষেতে তিনিই প্র-সেন।
বলা উচিত যে, ছড়া বানাবার কিছু অভ্যাস আমার ছিল। কিন্তু ছন্দের হিসেব রাখার বালাই ছিল না। কেন-না, আমি মনে করি, ছন্দ গোনার বিষয় নয়, শোনার বিষয়। চোখে ছন্দ দেখা যায় না, কানে শুনতে হয়। কোন রচনাটার কী ছন্দ, কোন বৃত্ত, কয় পর্ব বা মাত্রা, এসব শুনলেই আমার আতঙ্ক উপস্থিত হয়। এই নিয়ে আমার ছন্দো-পাওয়া সহপাঠী কবি-বন্ধুর (সে আবার অধ্যাপক মহাশয়ের পেয়ারের ছাত্র) সঙ্গে প্রায়ই হাতাহাতি হবার উপক্ৰম হত। একদিন অবসথা। চরমে পৌঁছোলা। আমার ক্ষমাগুণে সেদিন শান্তি রক্ষা হয়েছিল। সে একখণ্ড কাগজে আমাকে শাসিয়ে একটি ‘কবিতা” রচনা করে আমার দিকে ছুড়ে দিল। কবিতাটি এই :
ওরে হতভাগা হলধর পতিতুণ্ড।
মুখটি খুলিলেই গুড়িয়ে দেব মুণ্ড।
ফের যদি তুই বানাতে চাস রে ছন্দ,
সব লেখা একদম করে দেব বন্ধ।
এই কবিতা পড়ে আমার শুধু দম বন্ধ হবার নয়, পেট ফাটবারও উপক্ৰম হয়েছিল। কিন্তু কিছু না-বলে ক্ষমা করতে হল। কবি-বন্ধুর কথা দিয়ে কথা রাখার সৎসাহস সম্বন্ধে আমার কিছুমাত্ৰ সন্দেহ ছিল না। সহপাঠী বন্ধুরা একবাক্যে বললেন, এই কবিতাটির ছন্দ নির্ভুল, মাত্ৰাসংখ্যার হিসেব ঠিক আছে। কিন্তু আমার–
কান “তা শুনি গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া কহে—
‘নহে, নহে, নহে।’”
কান ও জ্ঞানের বিবাদভঞ্জন করতে না পেরে তখন থেকেই ছড়া বানানো একদম বন্ধ করে দিলাম। বন্ধুবরও আমার এই সত্যনিষ্ঠা ও নৈতিক সাহসের তারিফ করেছিল। তার এই গুণগ্রাহিতার প্রশংসা না করে পারিনি।
ছড়া বানানো বন্ধ করার আরও একটা কারণ ঘটেছে। অধ্যাপক মহাশয় একদিন ক্লাসে এসেই প্ৰবোধ সেনের আর-একখানি সদ্য-প্রকাশিত বই সকলের সামনে তুলে ধরলেন। তারপর চলল প্রশস্তি-বচন। আমি মনে মনে ভাবলাম৷- “এক রামে রক্ষা নাই, সুগ্ৰীব দোসর।”
বইটির নাম ছন্দ-পরিক্রমা। প্রথমে মনে হল, ছন্দ-পরিশ্রমা। অধ্যাপক মহাশয়ের নির্দেশে এই বইটাও নাড়াচাড়া করে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতে হল “ছন্দ-পণ্ডশ্রমা”। আমার মতো স্বভাবকবিকে ছন্দ বোঝাবার সমস্ত চেষ্টাই পণ্ডশ্রম, এ কথা স্বীকার করতে লজা নেই। বইটির প্রথমেই পরিভাষা, শেষেও তা-ই। পরিভাষার ইটপাটকেলে হোঁচটা খেতে-খেতে ক্ষতবিক্ষত হতে হয়। এগোনো আর হয় না। কোনও পরিভাষা কেন মানতে হবে বা কেন ছাড়তে হবে, তার যুক্তিজালে জড়িয়ে গিয়ে দিশেহারা হতে হয়। প্ৰবোধ সেনই একসময়ে ছন্দের তিন রীতির নাম দিয়েছিলেন- অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত। আর তিনিই বারবার নাম-বদল করে চলেছেন। এই বই পড়তে গিয়ে ডি.এল. রায়ের আর-একটা হাসির গান মনে পড়ে গেল :
“ছেড়ে দিলাম পথটা
বদলে গেল মতটা,
এমন অবস্থাতে পড়লে
সবারই মত বদলায়।”
এই মত-বদল নাম-বদলের পালা কবে শেষ হবে কে জানে। ততদিন ছন্দ শেখার ও ছন্দ লেখার কাজটা মুলতুবিই থাক না। তা ছাড়া যেটুকু সহজাত ছন্দবোধ আমার ছিল, এই বই পড়ে তা-ও ঘুলিয়ে গেল। সুতরাং ছড়া বানাবার অভ্যাস ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর উপায় কী?
এমন সময়ে কবিকঙ্কণের কবিতার ক্লাসে ঢুকে যেন দিব্যদৃষ্টি পেয়ে গেলাম। ছন্দতঙ্ক অ্যালার্জি কেটে গেল। উৎসাহিত হয়ে আগের সপ্তাহের রবিবাসরীয় আনন্দবাজার খুঁজে-পেতে বার করলাম। সে-সপ্তাহের কবিতার ক্লাসেও পাঠ নেওয়া গেল। দুই ক্লাসের পাঠ নিয়েই ছন্দবোধের কুয়াশা যেন অনেকটা কেটে গেল। আরও পাঠ নেবার জন্য মনটা উৎসুক হয়ে উঠেছে। আশা হয়েছে, পাঠ নেওয়া শেষ হলে ছন্দো-পাওয়া কবিবন্ধুকে একবার দেখে নিতে পারব। আর প্রবোধচন্দ্রের অন্ধভন্তু অধ্যাপক মহাশয়কেও…। না সে-কথা থাক। ইতিমধ্যে ভালো করে পাঠ নিয়ে রাখা দরকার। আর তা হাতে-কলমে হলেই ভালো। ভরসার কথা এই যে, অধ্যাপক সরখেল মহাশয়ের নাতি ও ভৃত্যটির ছড়া শুনে আমার সেই ছড়া বানাবার ছেড়ে-দেওয়া অভ্যাসটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এখন কবিতার ক্লাসের মনোযোগী ছাত্রের মতো পাঠ নিতেও পারব, প্রশ্ন করতেও পারব। প্রশ্নগুলি বোকার মতো না হলেই হল।
অধ্যাপক সরখেলের দৃষ্টান্ত নিয়েই নূতন ছড়া বানিয়ে প্রশ্ন করব :
স্বৰ্ণপাত্র নয় ওটা উধৰ্ব নীলাকাশে,
বিশ্বের আনন্দ নিয়ে পূৰ্ণচন্দ্ৰ হাসে।
এটা কোনরীতির ছন্দ? অক্ষরবৃত্তের? ভুল করিনি তো? এবার ছন্দের রীতিবদল করা যাক।
স্বৰ্ণপাত্র নয় সুনীল আকাশে,
পূর্ণিমা-চাঁদ হোথা সুখভরে হাসে।
এটা মাত্রাবৃত্ত তো? আমার কান তো তাই বলে। কর্ণধাররা কী বলেন, জানতে চাই। কানমলার ভয় যে একেবারেই নেই, তা বলতে পারি না। আবার রীতিবদল করা যাক :
সোনার থালা নয় গো ওটা
সুদূর নীলাকাশে,
বিশ্বপ্রাণে জাগিয়ে পুলক
পূৰ্ণিমা-চাঁদ হাসে।
এটাকে স্বরবৃত্ত ছন্দ বলা যায় কি? আমার কান তো তা-ই বলে। জ্ঞানের বিচারে কানের দণ্ডবিধান না হলেই বঁচি। জ্ঞানের এজলাসে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড়ালে প্ৰাণটাও ভয়ে কাঠ হয়ে যায়। হাকিমের রায় শূনে কানও অনেক সময়ে লাল হয়ে ওঠে। তবু অধ্যাপক সরিখেল মহাশয়ের পরীক্ষার হলে হাজির হয়েছি। যদি তার কাছে পাস-মার্কা পেয়ে যাই, তাহলে ছন্দো-পাওয়া কবি-বন্ধু ও প্রসেন-ভক্ত ছন্দঅধ্যাপককে…। না, এখনও সে-কথা বলবার সময় হয়নি। আগে তো কবিতার ক্লাসে রীতিমতো পাঠ নিতে হবে, প্রশ্নও করতে হবে সন্দেহ দূর করবার জন্য।
এবার মনের দুঃখে নিজের দুরবস্থার কথা ফলাও করে বলতে হল। ভবিষ্যতে সরখেল মহাশয়ের বিরক্তি ঘটাব না। সংক্ষেপেই প্রশ্ন করব।
কবিকঙ্কণের উত্তর
নাম যদিও জানা গেল না, তবু আমার বিন্দুমাত্ৰ সন্দেহ নেই যে, ‘জিজ্ঞাসু পড়ুয়া’ একজন পাকা ছান্দসিক। আমার ধারণা ছিল নেহাতই পাঠশালা খুলেছি, প্রথম পড়ুয়ারা যাতে ছন্দের ব্যাপারটাকে মোটামুটি ধরতে পারেন তার জন্যে সহজ করে। সব বুঝিয়ে বলব, জটিলতার পথে আদীে পা বাড়াব না। বাড়াবার সাধ্যও আমার নেই। একজন পাকা ছান্দসিক যে হঠাৎ সেই পাঠশালায় ঢুকে, পড়ুয়ার ছদ্মবেশে, পাটির উপরে বসে পড়বেন, এমন কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। তার পদার্পণে আমি কৃতাৰ্থ, কিন্তু ক্লাস নেবার কাজটা এবারে আরও কঠিন হয়ে উঠল।
‘জিজ্ঞাসু পড়ুয়া’ কিছু প্রশ্ন করেছেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তর আমি এখুনি দিচ্ছিনে। ভাবছি, গোলমেলে কেস হাতে এলেই ছোটো ডাক্তাররা যেমন বড়ো ডাস্তারের সঙ্গে কনসালট করেন, তেমনিই আমাকেও হয়তো বড়ো ডাক্তারের শরণ নিতে হবে। এ-ব্যাপারে। আমি যাঁকে সেরা ডাক্তার বলে মানি, তিনি কলকাতায় থাকেন না। উত্তর পেতে তাই হয়তো দেরি হবে।
ইতিমধ্যে একটা কথা অকপটে নিবেদন করি। সেটা এই যে, ‘জিজ্ঞাসু পড়ুয়া’ যদিও আমরা দারুণ প্ৰশংসা করেছেন, তবু আমি খুশি হতে পারছিনে। খুশি হতে পারতুম, যদি তঁর চিঠিতে শ্ৰীপ্ৰবোধচন্দ্ৰ সেন সম্পর্কে কোনও বক্লোক্তি না থাকত।
কথাগুলি আমার জানা নেই। প্রথম কথাগুলি যদি জেনে থাকি, তবে শ্ৰীযুক্ত সেনের কাছ থেকেই জেনেছি। পরে আরও দু-এক জন প্রখ্যাত ছান্দসিকের কাছে পরোক্ষে পাঠা নিয়েছি ঠিকই, কিন্তু শ্রীযুক্ত সেনের কাছে আমার ঋণের পরিমাণ তাতে লাঘব হয় না। এই স্বীকৃতির প্রয়োজন ছিল। ‘জিজ্ঞাসু পড়ুয়া’ যদি এর ফলে আমার উপরেও চটে যান, তো আমি নিরুপায়।
‘জিজ্ঞাসু পড়ুয়া’র চিঠি-২
সশ্রদ্ধ নিবেদন এই। যে শ্রদ্ধা নিয়ে আপনার কবিতার ক্লাসে আসন নিয়েছি, প্ৰত্যেক পাঠের পরে সে-শ্রদ্ধা ক্ৰমে বাড়ছে। গত রবিবারের পাঠ শুনে এবং আমার প্রশ্নের উত্তরে আপনার বক্তব্য জেনে আমার ছন্দবোধের কুয়াশা আরও অনেকখানি কেটে গেল। যাঁকে আমি ‘কবিঘাতক ছান্দসিক’ আখ্যা দিতেও কুষ্ঠাবোধ করিনি, আপনি সেই প্ৰবোধচন্দ্র সেনের প্রতি খুবই অনুকুল মনোভাব প্রকাশ করেছেন। চটে যেতাম, যদি আপনার সম্বন্ধে অটুট। শ্রদ্ধা না থাকত। তাই চটে না গিয়ে তঁর সম্বন্ধে আমার মনোভাবটা ঠিক কি না তা-ই যাচাই করে দেখতে হল। আপনার শেষ পাঠের সঙ্গে প্ৰবোধচন্দ্রের ‘ছন্দ পরিক্রমা’ বইটির মতামতটা মিলিয়ে দেখলাম। অক্ষরবৃত্ত ছন্দ সম্বন্ধে দুইজনের মতের মিল দেখে আমার বক্লোক্তিগুলির জন্য একটু কুষ্ঠাবোধই হল। এই বইটির দ্বিতীয় অধ্যায়ে অক্ষরবৃত্তের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি দিয়েছেন :
“পশমী শাল গায়ে দিয়ে
গেলাম কাশ্মীরে,
রেশমী জামা-গায়ে শেষে
আগরা এনু ফিরে।”
আপনার দৃষ্টান্তগুলির মিল দেখে অবাক হয়ে গেলাম। দুই জনের হিসাব দেবার রীতিতেও যথেষ্ট মিল। … কিন্তু একটা জায়গায় একটু খটকা লাগল। রবীন্দ্রনাথের ‘বাঁশি’ কবিতায় আছে :
“আকবর বাদশার সঙ্গে
হরিপদ কেরানির কোনো ভেদ নেই।”
এখানে ‘আকবর’ শব্দে। আপনি ধরেছেন তিন মাত্রা, ‘বাদশার’ শব্দেও তাই। ‘বাঁশি’ কবিতাটি পড়ে আমার মনে হল, ওই দুই শব্দে চার-চার মাত্ৰাই ধরা হয়েছে। কেন-না, ওই কবিতাটিতে টিকটিকি, ট্রামের খরচা, মাছের কানকা’, ‘আধমরা’ প্রভৃতি সব শব্দেরই মধ্যবর্তী হসবৰ্ণকে একমাত্রা বলে ধরা হয়েছে, কোথাও ব্যতিক্ৰম নেই। সুতরাং ‘আকবর’ ও ‘বাদশা’ শব্দের ক ও দ-কে একমাত্রা হিসেবে ধরা হবে। না কেন?
সবশেষে বলা উচিত যে, এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য কবিতা-ক্লাসের সহায়তা করা, বাধা সৃষ্টি করা নয়। প্ৰবোধচন্দ্রও তীর ছন্দ-পরিক্রমা” বইটির নিবেদন অংশে জিজ্ঞাসু ছাত্রের প্রশ্নকে তাঁর চিন্তার সহায়ক বলেই স্বীকার করেছেন। তাই আশা করি আপনিও আমার প্রশ্নকে সেভাবেই গ্ৰহণ করবেন। ইতি ২০ আশ্বিন ১৩৭২।
অনুলেখ : আজকের পাঠের একটি দৃষ্টান্ত সম্বন্ধেও মনে একটা প্রশ্ন জেগেছে। সেটাও নিবেদন করি।–
‘কালকা মেলে টিকিট কেটে সে
কাল গিয়েছে পাহাড়ের দেশে।’
এটা অক্ষরবৃত্ত রীতিতে পড়তে গিয়ে যতটা কানের সায় পেয়েছি, তার চেয়ে বেশি সায় পেয়েছি স্বরবৃত্ত রীতিতে পড়ে। এরকম সংশয়স্থলে কী করা উচিত? ইতি ২৩ আশ্বিন ১৩৭২।
কবিকঙ্কণের উত্তর :
গত সপ্তাহের রবিবাসরীয় আলোচনীতে ‘জিজ্ঞাসু পড়ুয়া’র চিঠি পড়লুম।
(১) তাঁকে যে আমি প্ৰবোধচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করতে পেরেছি আপাতত এইটেই আমার মস্ত সাফল্য।
(২) ‘ছন্দ-পরিক্রমা’ আমি এখনও পড়িনি। পড়তে হবে। ছন্দ নিয়ে যখন আলোচনা করতে বসেছি, তখন প্ৰবোধচন্দ্রের সব কথাই আমার জানা চাই। শুনেছি প্ৰবোধচন্দ্ৰ এখন বাংলা কবিতার মূল ছন্দ তিনটির অন্য প্রকার নামের পক্ষপাতী। কেন, তা আমি জানিনে। জানতে হবে। ছিন্দ-পরিক্রমা” গ্রন্থে ব্যক্ত মতামতের সঙ্গে আমার ধারণার যদি বিরোধ না ঘটে, তবে সে তো আমার পক্ষে পরম শ্লাঘার বিষয়।
(৩) ‘বাঁশি’ কবিতার লাইন দুটির প্রসঙ্গে জানাই, স্মৃতি আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমার স্মৃতিতে লাইন দুটির স্বাতন্ত্র্য বজায় ছিল না, তারা এক হয়ে গিয়েছিল, এবং সেইভাবেই, অর্থাৎ টানা লাইন হিসেবে, তাদের আমি উদ্ধৃত করেছিলাম। টানা লাইন হিসেবে গণ্য করলে দেখা যাবে, ‘আকবর’ ও ‘বাদশার’— এই দুই শব্দের কাউকেই তিন-মাত্রার বেশি মূল্য দেওয়া যায় না। দোষ আমার বিচারের নয়, অসতর্কতার।
কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ‘আকবর বাদশার সঙ্গে’- এই লাইনটিকে যদি পরবর্তী লাইনের সঙ্গে জুড়ে না-ও দিই, অর্থাৎ তাকে যদি আলাদাই রাখি, তবে তাতেই কি নিঃসংশয় হওয়া যায় যে, ‘আকবর’ ও ‘বাদশার’— এরা চার-মাত্রারই শব্দ? বলা বাহুল্য, পুরো লাইনটিকে দশ-মাত্রার মূল্য দিলে তবেই এরা চার-চার মাত্রার শব্দ হিসেবে গণ্য হবে। জিজ্ঞাসু পড়ুয়া সে-দিক থেকে ন্যায্য কথাই বলেছেন। কিন্তু পুরো লাইনটির মাত্ৰা-সংখ্যা যে দশের বদলে আটও হতে পারে, এমন কথা কি ভাবাই যায় না? যে-ধরনের বিন্যাসে এই কবিতাটি লেখা, সেই ধরনের বিন্যাসে রবীন্দ্ৰনাথ অনেক ক্ষেত্রে চার-মাত্রা কিংবা আট-মাত্রার লাইন রাখতেন। ‘বাঁশি’ কবিতাটিতেও আট-মাত্রার লাইন অনেক আছে।
মুশকিল এই যে, ‘আকবর বাদশার সঙ্গে’- এই লাইনও যে সেই গোত্রের, অর্থাৎ আট-মাত্রার, তা-ও আমি জোর করে বলতে পারছিনে। জিজ্ঞাসু পড়ুয়া এটিকে দশ-মাত্রার মূল্য দিয়েছেন : দিয়ে ‘আকবর’ এবং বাদশার’— এই শব্দ দুটিকে চার-চার মাত্রার শব্দ বলে গণ্য করেছেন। তিনি ভুল করেছেন, এমন কথা বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। শুধু অনুরোধ জানাই, তিনিও একবার ভেবে দেখুন, পুরো লাইনটিকে আট-মাত্রার মূল্য দিয়ে, যদি কেউ ওই শব্দ দুটিকে তিন-তিন মাত্রার শব্দ হিসেবে গণ্য করে, তবে সেটা অন্যায় হবে কি না।
জিজ্ঞাসু পড়ুয়া অবশ্য তাঁর সিদ্ধান্তের সপক্ষে একটি জোরালো যুক্তি দিয়েছেন। সেটা এই যে, ওই কবিতাটিতে “সব শব্দেরই মধ্যবর্তী হস্বৰ্ণকে এক-মাত্রা বলে ধরা হয়েছে, কোথাও ব্যতিক্ৰম নেই।” সুতরাং ‘আকবর’ ও ‘বাদশার’ শব্দের মধ্যবর্তী ‘ক’ ও ‘দ’-কেও একটি করে মাত্রার মূল্য দেওয়া উচিত।
ঠিক কথা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি এমন কবিতা লেখেননি, যাতে শব্দের মধ্যবর্তী হস্বৰ্ণ কোথাও-বা মাত্রার মূল্য পায়, কোথাও-বা পায় না? এমন কথা কেমন করে বলি? “আরোগ্য’ গ্রন্থের ‘ঘণ্টা বাজে দূরে” কবিতাটি দেখা যাক। সেখানে দেখছি, “হেথা হোথা চরে গোরু শস্যশেষ বাজরার খেতে’- এই লাইনটিতে বাজরার” শব্দের মধ্যবর্তী জ’-কে একটি মাত্রার মূল্য দিতে হয় বটে, কিন্তু তার পরের লাইনেই (“তরমুজের লতা হতে”) তরমুজ শব্দের মধ্যবতী ‘র’-কে মাত্রার মূল্য দিতে হয় না।
বলা বাহুল্য, এতেই প্রমাণিত হয় না যে, ‘ঘণ্টা বাজে দূরে কিংবা অন্যান্য কবিতায় যে-হেতু ব্যতিক্ৰম আছে, অতএব বাঁশি’ কবিতাতেও ব্যতিক্ৰম আছে, এবং “আকবর বাদশার সঙ্গে”- এই লাইনটিকেও আট-মাত্রার লাইন হিসেবে গণ্য করে। ‘ক’ আর “দ”-কে মাত্রার মূল্য থেকে বঞ্চিত করতেই হবে। না, এমন অদ্ভুত দাবি আমি করি না। বরং বলি, সম্ভবত জিজ্ঞাসু পড়ুয়ার কথাই ঠিক, সম্ভবত ‘আকবর’ ও বাদশার’— এরা চার-চার মাত্রার শব্দই বটে। কিন্তু একই সঙ্গে অনুরোধ জানাই, অন্য রকমের বিচারও সম্ভব কি না, জিজ্ঞাসু পড়ুয়া যেন সেটাও একবার সহৃদয় চিত্তে ভেবে দেখেন।
ইতিমধ্যে আর-একটা কথা বলা দরকার। অক্ষরে-অক্ষরে অসবর্ণ মিলনের দৃষ্টান্ত হিসেবে জিজ্ঞাসু পড়ুয়ার দরবারে ‘আকবর’ এবং বাদশার যদি একান্তই পাস-মার্ক না পায়, তাহলে রবীন্দ্রকাব্য থেকেই আর-একটি দৃষ্টান্ত আমি পেশ করতে পারি। “জন্মদিনে” গ্রন্থের “ঐকতান” কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন “ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে শৌখিন মজদুরি।” মজদুরি’ শব্দটিতে “জীয়ে দিয়ে অসবর্ণ মিলন ঘটেছে, জিজ্ঞাসু পড়ুয়া এ কথা আশা করি স্বীকার করবেন। শব্দটিকে কোনওক্রমেই তিন-মাত্রার বেশি মূল্য দেওয়া সম্ভব নয়। এমন দৃষ্টান্ত আরও কিছু আমার সংগ্রহে আছে।
(৪) “কালকা মেলে. পাহাড়ের দেশে”- এই লাইন দুটিকে অক্ষরবৃত্ত রীতিতে পড়ে কনের যতটা সায় পাওয়া যায়, তার চাইতে বেশি সায় যদি পাওয়া যায় স্বরবৃত্ত রীতিতে, তবে তো বুঝতেই হবে যে, শব্দের বিন্যাসে আমার আরও কুঁশিয়ার থাকা উচিত ছিল। প্রসঙ্গত জিজ্ঞেস করি, জিজ্ঞাসু পড়ুয়া তীর চিঠিতে প্ৰবোধচন্দ্রের গ্রন্থ থেকে অক্ষরবৃত্তের দৃষ্টান্ত হিসেবে, যে-দুটি লাইন তুলে দিয়েছেন (“পশমী শাল.আগরা এনু ফিরে”), তাদেরও কি স্বরবৃত্ত রীতিতে পড়া যায় না? এ-সব ক্ষেত্রে পাঠকের বিভ্ৰাট ঘটে। মূলত শব্দের গাঁটের জন্য। গাঁটগুলিকে অক্লেশে পেরোতে পারলে যা অক্ষরবৃত্ত, হোঁচটি খেলে তাকেই অনেকসময়ে স্বরবৃত্ত বলে মনে হয়। যদি সম্ভব হয়, এই গাঁটগুলি নিয়ে পরে আলোচনা করব।
ড. ভবতোষ দত্তের চিঠি
সবিনয় নিবেদন, আপনার ‘কবিতার ক্লাস’-এর আমি একজন উৎসুক পড়ুয়া। কবিতার ক্লাস প্রায় শেষ হয়ে এল। আপনার শেষের দুটি ক্লাস সম্বন্ধে আমার দু-একটি কথা মনে হয়েছে। নিবেদন করি।
স্বরবৃত্ত ছন্দ যে চার সিলেবল-এর কম অথবা বেশি স্বীকার করে, এ-কথা। আপনি নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন। আপনার দেওয়া দৃষ্টান্ত কয়টি লক্ষ করলাম— হয় তারা মৌখিক ছড়া অথবা ইয়ে-শব্দযুক্ত কাব্যপঙক্তি। ইয়েকে যুগ্মস্বর ছাড়া কী বলা যায় ইংরেজি ডিপথং-এর মতো। বাংলাতেও ঐ অথবা ঔ-এর মতো। আমার ধারণা, আপনি রবীন্দ্রনাথ অথবা সত্যেন্দ্রনাথের অথবা আধুনিক কোনও কবির কবিতায় চার সিলেবল-এর ব্যতিক্রম পাবেন না। কিংবা পেলেও সেটা এতই বিরল যে, তাকে স্বরবৃত্ত ছন্দের সাধারণ প্রকৃতি বলে নির্দেশ করতে পারেন না। ছড়ার ছন্দে যে-সব দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তা যদি এর সাধারণ প্রকৃতিই হত, তবে পরবর্তী আদর্শ শিল্পী-কবিরা তার ব্যবহার নিশ্চয়ই করতেন। তাঁরা চার সিলেবল-এর পর্বকেই আদর্শরূপে গণ্য করেছেন। তার অর্থ নিশ্চয়ই এই যে, পাঠযোগ্য কবিতায় বাঙালির উচ্চারণ-প্রকৃতি চার সিলেবলকেই স্বীকার করে মাত্র।
আপনি বলেছেন, স্বরবৃত্ত ছন্দ গানের সুরের ছন্দ। ছড়া ইত্যাদিতে মধ্যযুগে ব্যবহৃত এই-জাতীয় ছন্দকে ছড়ার ছন্দই বলা উচিত; সেকালে একে ধামালী ছন্দ বলা হত। রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ-ব্যবহৃত এই ছন্দের আধুনিক শিল্পসম্মত রূপকেই খাঁটি স্বরবৃত্ত বলা উচিত। মধ্যযুগের ধামালী অযত্নকৃত- এর প্রকৃতি সম্বন্ধে কেউ অবহিত ছিলেন না। সে-জন্য তিন সিলেবল বা পাঁচ সিলেবল নিয়ে কেউ মাথা ঘামাননি। বিশেষত কোনও বড়ো প্রধান গুরু কাব্যেই এই ছন্দের ব্যবহার নেই।
ছড়া সুরে উচ্চারিত হত, এ-কথা সত্য। আপনি বলেছেন, স্বরবৃত্ত ছন্দ এই জন্যই গানের ছন্দ। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, সুরে গাওয়া বা উচ্চারিত হত না হেন বস্তু মধ্যযুগে ছিল না। বৈয়ব পদাবলির কথা ছেড়ে দিন, বৃহৎকায় মঙ্গলকাব্যগুলিও সুর করে পড়া হত। মঙ্গলকাব্য তো স্বরবৃত্ত ছন্দে লেখা হত না, হত অক্ষরবৃত্ত ছন্দে। কিন্তু এখানেও বলতে পারি, ভারতচন্দ্রের আগে অক্ষরবৃত্ত পয়ার ছন্দেও চোদ্দ অক্ষরের (বা মাত্রার) নানা ব্যতিক্রম হামেশাই দেখা যেত। সেজন্যে কি বলবেন ব্যতিক্ৰমটাই সাধু পয়ার রীতির প্রকৃতি? অক্ষরবৃত্তও গানের সুরেরই ছন্দ? এর পরবর্তী সিদ্ধান্ত, ছন্দ মাত্রেই গানের সুর থেকে উদ্ভূত। সেটা অবশ্য আলাদাভাবেই আলোচ্য।
স্বরবৃত্ত ছন্দের বিশেষত্ব হচ্ছে এর হসন্ত-প্ররণত। হসন্ত-ধ্বনি থাকার জন্যই শব্দের প্রথমে ঝোক পড়ে। শব্দের প্রথম দিকে ঝোক এবং শব্দের প্রান্তের হসন্ত-ধ্বনি চলিতভাষারও বিশেষত্ব। এ বিষয়ে খুব একটা মতভেদের অবকাশ আছে বলে মনে করি না। বস্তৃত স্বরবৃত্ত ছন্দের হসন্ত-প্রবণতা ভাষার মৌখিক রীতির জন্যই। রবীন্দ্ৰনাথ বলেছিলেন—
‘চলতি ভাষার কবিতা বাংলা শব্দের স্বাভাবিক হসন্তরূপকে মেনে নিয়েছে।’
এটা লক্ষ্য করলে গানের সুর থেকে স্বরবৃত্ত ছন্দের উদ্ভব হয়েছে। এ-কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। চলতি মুখের ভঙ্গি আর সুরের ভঙ্গি সম্পূর্ণ আলাদা বস্তু। একটাতে থাকে বেঁক, আর-একটাতে প্রবাহ। ইতি ২৪, ৩, ৬৬
কবিকঙ্কণের উত্তর :
সবিনয় নিবেদন,
আপনার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি। উত্তর লিখতে অসম্ভব দেরি হল, তার জন্য মার্জনা চাই।…
আপনার প্রতিটি কথাই ভাববার মতো। তা ছাড়া, এমন অনেক তথ্য আপনি জানিয়েছেন, যা আমার জানা ছিল না। জেনে লাভবান হয়েছি। শুধু একটি ব্যাপারে। আমার একটু খটকা লাগছে। স্বরবৃত্তে রচিত “পাঠযোগ্য কবিতায় বাঙালির উচ্চারণ প্রকৃতি” যে শুধু চার সিলেবল-এর পর্বকেই স্বীকার করে, এই সিদ্ধান্তের যুক্তি হিসেবে আপনি জানিয়েছেন, “রবীন্দ্রনাথ অথবা সত্যেন্দ্রনাথের অথবা আধুনিক কোনও কবির কবিতায় চার সিলেবল-এর ব্যতিক্ৰম” পাওয়া যাবে না। “কিংবা পেলেও সেটা এতই বিরল যে, তাকে স্বরবৃত্ত ছন্দের সাধারণ প্রকৃতি বলে নির্দেশ” করা উচিত হবে না।
অনুমান করি, আপনি যেহেতু “পাঠযোগ্য” কবিতার উপরে জোর দিতে চান, তাই—ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত হিসেবে— ‘মৌখিক ছড়ার দৃষ্টান্ত আপনার মনঃপূত নয়।
এ-বিষয়ে আমার বক্তব্য সংক্ষেপে সবিনয়ে নিবেদন করি।
(১) ‘মৌখিক ছড়াগুলি তো একালে শুধুই মুখে-মুখে ফেরে না, লিপিবদ্ধও হয়ে থাকে। এককালে সেগুলি হয়তো শুধুই কানে শোনবার সামগ্ৰী ছিল, এখন সেগুলিকে আকছার চোখে দেখছি। এবং পড়ছি। অগত্যা তাদের আর ‘পাঠযোগ্য’ সামগ্ৰী হিসেবেও গণ্য না-করে উপায় নেই। তবে আর সেগুলিকে দৃষ্টান্ত হিসেবে ব্যবহার করায় আপত্তি কেন?
(২) ‘বাঙালির উচ্চারণ-প্রকৃতি’র পক্ষে সত্যিই কি স্বরবৃত্তে শুধুই চার সিলেবল-এর পর্বকে স্বীকার করা সম্ভব? সর্বত্র সম্ভব? ক্ৰমাগত যদি চার-চারটি ক্লোজড সিলেবল দিয়ে আমরা পর্ব গড়তে চাই, পারব কি?
(৩) রবীন্দ্রনাথ কিংবা সত্যেন্দ্রনাথ স্বরবৃত্তকে প্রধানত কীভাবে ব্যবহার করেছেন, সেটা আমার বিচার্য ছিল না; স্বরবৃত্তকে কীভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, সেইটেই ছিল আমার দেখবার বিষয়। দেখতে পাচ্ছি, ছয় থেকে দুয়ে এর ওঠানামা। কাজিফুল ‘কুড়োতে কুড়োতে” আমরা ছয়ে উঠতে পারি, আবার ঝুপকুপা’ করে দুয়ে নামতে পারি। উচ্চারণে যে-ছন্দ ইলাসটিসিটিকে এতটাই প্রশ্রয় দেয়, তাকে ঠিক কবিতার ছন্দ বলতে আমার বাধে। ডিপথং-এর কথাটা আমি ভেবে দেখেছি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই ওঠানামার সর্বত্র ব্যাখ্যা মেলে না। বরং সন্দেহটা ক্ৰমেই পাকা হয়ে দাঁড়ায় যে, নিজেদের অগোচরে পর্বকে কখনও আমরা টেনে বড়ো করি, কখনও-বা অতিদ্রুত উচ্চারণে তাকে কমিয়ে আনি। শব্দের উচ্চারণে হ্রাসবৃদ্ধির এতখানি স্বাধীনতা কবিতার ব্যাকরণ স্বীকার করে কি?
পরিশেষে বলি, সম্ভবত আপনার কথাই ঠিক। তবু অনুরোধ করি, আমার কথাটাও দয়া করে একবার ভেবে দেখবেন। আপনি সহূদয় পাঠক। উপরন্তু যুক্তিনিষ্ঠ। সেইজন্যেই এই অনুরোধ।…
সপ্রীতি শুভেচ্ছা জানাই। ইতি।
কবি শ্ৰীশঙ্খ ঘোষের চিঠি
কাজটা কি ভালো করলেন? এতো সহজেই যে ছন্দ-কাণ্ডটা জানা হয়ে যায়, এটা টের পেলে ছেলেমেয়েরা কি আর স্কুল-কলেজের ক্লাস শুনবে? ক্লাস মানেই তো সহজ জিনিসটিকে জটিল করে তুলবার ফিকির।
এ-লেখার এই একটি কৌশল দেখছি যে, আপনি শুরু করতে চান সবার-জানা জগৎ থেকে। তাই এখানে ‘যুক্তাক্ষর’ কথাটিকে ব্যবহার করতে একটুও দ্বিধা করেননি, দেখিয়েছেন কোন ছন্দে এর কীরকম মাত্রা মূল্য। বোঝানোর দিক থেকে এ একটা উপকারী পদ্ধতি।
কিন্তু এর ফলে ছোটো একটি সমস্যাও কি দেখা দেবে না? যুক্তাক্ষর তো শব্দের চেহারা-বৰ্ণনা, তার ধ্বনিপরিচয় তো নয়। ছন্দ যে চোখে দেখবার জিনিস নয়, কানে শুনবার- এটা মনে রাখলে ধ্বনিপরিচয়টাই নিশ্চয় শেষ পর্যন্ত আমাদের কাজে লাগবে? যেমন ধরা যাক, ছন্দ” শব্দটি। মাত্রাবৃত্তে যুক্ত-অক্ষর দু-মাত্রা পায়। এখন এ-শব্দটি যদি মাত্রাবৃত্তে থাকে তো দু-মাত্রার মূল্য দেব এর কোন অংশকে? যুক্তাক্ষর ‘দ’-কে, নাকি বুদ্ধিদল ছিন’-কে? মাত্রার হিসেবটা কেমন হবে? ১+২ (ছ+ন্দ), না ২+১ (ছন + দ)? চোখ বলবে প্রথমটি, কান বলবে দ্বিতীয়।
তাহলে দল বা সিলেবল কথাটাকে এড়িয়ে থাকা মুশকিল। কিন্তু বেশ বোঝা যায়, আপনি ইচ্ছে করেই অল্পে-আল্পে এগিয়েছেন। স্বরবৃত্ত আলোচনার আগে একেবারেই তুলতে চাননি সিলেবল-এর প্রসঙ্গ।
আর সেইজন্যেই মাত্রাবৃত্তের একটি নতুন সূত্রও আপনাকে ভাবতে হল। শব্দের আদিতে না থাকলে এ-ছন্দে যুক্তাক্ষর দু-মাত্রা হয়! আপনি এর সঙ্গে আরও একটু জুড়ে দিয়ে বলেছেন যে, শব্দের ভিতরে থাকলেও কখনও কখনও যুক্তাক্ষর একমাত্রিক হতে পারে। কোথায়? যেখানে তার ঠিক আগেই আছে হস্বৰ্ণ কিংবা যুক্তস্বর। আপনি বলবেন, ‘আশ্লেষ’ শব্দের ‘শ্নে’ আর সংশ্লেষ’ শব্দের ‘শ্লে’মাত্রাবৃত্তে দু-রকম মাত্রা পাচ্ছে। প্রথমটিতে দুই, পরেরটিতে এক। অথবা বলবেন এ-ছন্দে সমান-সমান হয়ে যায়। ‘চৈতী’ ‘চৈত্র’?
ঠিক কেন যে তা হচ্ছে, এ-ও আপনি জানেন। জানেন যে, এ-সব ক্ষেত্রে সিলেবল দিয়ে ভাবলে ব্যাপারটাকে আর ব্যতিক্ৰম মনে হয় না, মনে হয় নিয়মেরই অন্তর্গত। যদি এভাবে বলা যায় যে, মাত্রাবৃত্তে বুদ্ধদল দু-মাত্রা পায়, মুক্তদল এক-মাত্ৰা— তাহলেই ওপরের উদাহরণগুলির একটা সহজ ব্যাখ্যা মেলে। উদাহরণের দিক থেকে দেখলে শব্দগুলি তো ‘সং + শ্লেষ’, ‘আস+ লেষ’ ‘চৈ + তী’ ‘চৈৎ + ‘র’- এইরকম দাঁড়ায়?
কিন্তু সেভাবে আপনি বলতে চান না; চান না যে, সিলেবল-এর বোঝাটা গোড়া থেকেই পাঠকের ঘাড়ে চাপুক। যুক্তাক্ষর বলেই যদি কাজ মিটে যায় তো ক্ষতি কী! ফলে আপনি তো দিব্যি টগবগিয়ে চলে গেলেন, কিন্তু ক্লাসে যারা ছন্দ পড়াবেন। তাদের কী দশা হবে?
কবিকঙ্কণের উত্তর
প্রতিভাজনেষু,
শঙ্খ, আপনার চিঠি পেয়ে বড়ো ভালো লাগল।
সত্যি, আমি ঠিকই করেছিলুম যে, সিলেবিক ছন্দ স্বরবৃত্তের এলাকায় ঢুকবার আগে সিলেবল-কথাটা মুখেও আনিব না। আমার ভয় ছিল, ছন্দের ক্লাসের যাঁরা প্রথম পড়ুয়া, গোড়াতেই যদি ‘মোরা’ সিলেবল ইত্যাদি সব জটিল তত্ত্ব তাঁদের বোঝাতে যাই, তাহলে তাঁরা পাততাড়ি গুটিয়ে চম্পট দেবেন। কিন্তু ‘অক্ষর’ সম্পর্কে সেই ভয় নেই। অক্ষর তারা চেনেন। তাই, প্ৰাথমিক পর্যায়ে, অক্ষরের সাহায্য নিয়ে আমি তাদের ছন্দ চেনাবার চেষ্টা করেছি। তবু, তখনও আমি ইতস্তত বলতে ভুলিনি যে, ধ্বনিটাই হচ্ছে প্রথম কথা; বলেছি যে, চোখ নয়, কানই বড়ো হাকিম। এমনকি, এ-ও আমি স্পষ্ট জানিয়েছি যে, অক্ষর আসলে ধ্বনির প্রতীক- মাত্র। ‘কবিতার ক্লাস’-এর পাণ্ডুলিপি তো আপনি দেখেছেন। অক্ষর ও ধ্বনি-বিষয়ক এসব মন্তব্য নিশ্চয় আপনার চোখ এড়ায়নি।
যুক্তাক্ষরের রহস্যটা আপনি ঠিকই ধরেছেন। এবং যেভাবে সেই রহস্যের আপনি মীমাংসা করেছেন, তাতে সমস্ত সংশয়ের নিরসন হওয়া উচিত। কিন্তু আপনি কি নিশ্চিত যে, ‘চৈত্র’কে চৈৎ + র’ হিসেবে বিশ্লিষ্ট করেই আপনি নিস্কৃতি পাবেন? বুদ্ধ সিলেবল চৈৎ কে আপনি দু-মাত্রার মূল্য দিচ্ছেন, মুক্ত সিলেবল রিকে দিচ্ছেন এক-মাত্রার। ফলত সব মিলিয়ে এই শব্দটি তিন-মাত্রার বেশি মূল্য পাচ্ছে না। আপনার এই হিসেবে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু কারও-কারও হয়তো আপত্তি থাকতে পারে। “মাত্রাবৃত্তে বুদ্ধিদল দু-মাত্রা পায়, মুক্তদল একমাত্ৰা”, এই বিধান মেনে নিয়েও তাঁরা প্রশ্ন তুলতে পারেন যে, চৈত্র’ কি বস্তৃত একটি বুদ্ধিদল ও একটি মুক্তদলের সমষ্টি? তারা দাবি করতে পারেন যে, চৈত্র’কে আসলে চ + ইৎ + ‘র হিসেবে বিশ্লিষ্ট করা উচিত, এবং সেই অনুযায়ী এই শব্দটিকে মোট চার-মাত্রার মূল্য দিতে হবে। (প্রথম ও শেষের দুটি মুক্তদলের জন্য দ-মাত্রা ও মধ্যবর্তী একটি বুদ্ধিদলের জন্য দু-মাত্রা।) সৈন্য’ দৈন্য ‘মৈত্রী’ ‘বৌদ্ধ’ ইত্যাদি শব্দের বেলাতেও আপনার হিসেবের বিরুদ্ধে এই একই রকমের দাবি উঠতে পারে। আপনি এদের সৈন্য + নি, দৈন্য + নি, মৈৎ + রী, বৌদ + ধ হিসেবে দেখাবেন। তাঁরা দেখাবেন স + ইন্ + ন, দ + ইন্ + ন, ম + ইৎ + রী, ব +উদ্ + ধ হিসেবে। আপনি এদের একভাবে বিশ্লিষ্ট করবেন; তারা করবেন আর-একভাবে।
আমি অবশ্য আপনার পন্থাতেই এসব শব্দকে বিশ্লিষ্ট করবার পক্ষপাতী। তার কারণ, আমি জানি যে, যুক্তস্বরের পরে হস্বৰ্ণ থাকলে (সেই হিসাবর্ণটি যুক্তাক্ষরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকলেও কিছু যায়-আসে না)। ধ্বনিসংকোচ আনিবাৰ্য হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ এ-তথ্য অনেক আগেই জেনেছিলেন। তিনি ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন যে, মাত্রাবৃত্তে ‘পৌষকে পুরো তিন-মাত্রার মূল্য দেওয়া চলে না; নইলে চিত্রা’ গ্রন্থের ‘সিন্ধুপারে কবিতায় (যা কিনা মাত্রাবৃত্তে লেখা) ‘পৌষ-শব্দটার চলতি বানান ছেড়ে তিনি “পউষ, প্রখর শীতে জর্জর..” লিখতে গেলেন কেন? উদ্দেশ্য যে পৌষ-এর উচ্চারণকে আর-একটু বিবৃত করে নিশ্চিন্ত চিত্তে ওকে তিন-মাত্রার পার্বণী ধরিয়ে দেওয়া, তাতে আমার সন্দেহ নেই।
বুঝতেই পারছেন, যুক্তাক্ষর-রহস্যের মীমাংসা যদি আমি সিলেবল ভেঙে করতে যৌতুম, তাহলে, প্রসঙ্গত, এসব প্রশ্ন উঠত। শব্দের বিশ্লেষণ-পদ্ধতি নিয়ে তর্ক বাধত। ধন্ধ দেখা দিত। ছন্দের প্রথম-পড়ুয়াকে সেই ধন্ধ থেকে আমি দূরে রাখতে চেয়েছি। যেভাবে বোঝালে তাঁরা চটপট ধরতে পারবেন, প্রাথমিক ব্যাপারগুলিকে সেইভাবেই তাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছি।
বাকিটা আপনারা বোঝান। আপনার ভাষায় দিব্যি টগবগিয়ে আমি চলে গেলুম। কিন্তু যাবার আগে, চৌরাস্তায় ড়ুগড়ুগি বাজিয়ে যেসব পড়ুয়া আমি জোগাড় করেছিলুম, আপনাদের ওই ক্লাসঘরের মধ্যেই তাদের আমি ঢুকিয়ে দিয়ে এসেছি। এবারে আপনাদের পন্থায় আপনারা তাদের গড়েপিটে নিন। আমার পড়ুয়াদের আমি চিনি। তাই হলফ করে বলতে পারি, যে-পন্থাতেই পড়ান, তাদের নিয়ে বিন্দুমাত্র বেগ আপনাদের পেতে হবে না।