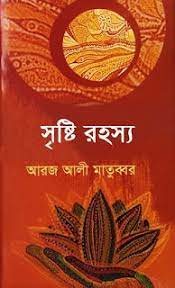- বইয়ের নামঃ সৃষ্টি রহস্য
- লেখকের নামঃ আরজ আলী মাতুব্বর
- বিভাগসমূহঃ দর্শন
০. নিবেদন (সৃষ্টি রহস্য)
সৃষ্টি রহস্য
রচনাকাল ১৯. ৪. ১৩৭২– ২৫. ৪. ১৩৭৭
প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৩৮৪
নিবেদন
বর্তমান দুনিয়ায় যেমন বহু জাতি বা সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ বাস করে, আদিকালেও তেমন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সভ্যাসভ্য বহু জাতি বা সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করিত এবং সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে উহাদের মতামতও ছিল বহুবিধ। প্রত্যেক দলের মানুষই তাহাদের আপন দলীয় মতকে মনে করিত সনাতন মত এবং উহা আজও করিয়া থাকে। অথচ উহাদের অনেকেই আপন দলীয় মতের বাহিরে অন্যদের মতবাদের কোনো খবর রাখিতে চাহেন না অথবা রাখিলেও তাহাতে গুরুত্ব দেন না। বলা বাহুল্য যে, সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে পৃথিবীতে যত রকম মতবাদ প্রচলিত আছে, নিশ্চয়ই তত রকম ভাবে কোনো কিছুর সৃষ্টি হয় নাই, সৃষ্টি হইয়াছে একই রকম ভাবে। কিন্তু কোন্ রকম? সাম্প্রদায়িক মনোভাব লইয়া কোনো ব্যক্তির পক্ষেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে কোনো ধর্ম বা সম্প্রদায় নিরপেক্ষ মানুষ পাওয়া কঠিন। এমতাবস্থায় বিভিন্ন মতবাদ সম্বন্ধে কিছু কিছু ওয়াকেফহাল হইয়া তত্ত্বানুসন্ধানী ব্যক্তিগণ যাহাতে একটি স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন, তজ্জন্য এই পুস্তকের প্রথম দিকে জগত ও জীবন সৃষ্টির বিষয়ে আদিম মানবদের সৃষ্টিতত্ত্ব, ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্ব, দার্শনিক মতে সৃষ্টিতত্ত্ব এবং বিজ্ঞান মতে সৃষ্টিতত্ত্বের সারাংশ সন্নিবেশিত হইল।
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধু যে জগত ও জীবন সৃষ্টির বিষয়েই মতভেদ আছে তাহাই নহে, মতভেদ মানব সমাজের আচার-অনুষ্ঠান, ধর্ম, রীতি-নীতি, সংস্কার-কুসংস্কার ইত্যাদিতেও। তাই মানব সমাজের কতিপয় সম্প্রদায়ের আচার-অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির উৎপত্তি সম্বন্ধেও কিছু কিছু বিবরণ দেওয়া হইল এই পুস্তকখানির শেষের দিকে।
মানুষের জাতিগত জীবন ব্যক্তিজীবনেরই অনুরূপ। ব্যক্তিজীবনে যেমন শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য আছে, জাতিগত জীবনেও তেমন শৈশব, বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য আছে। তবে জাতিগত জীবনের এখন সবেমাত্র যৌবনকাল, বার্ধক্য বহুদূরে। শৈশব ও বাল্যে মানুষ থাকে অনুকরণশীল ও অনুসরণশীল এবং কতকটা কৈশোরেও। সরলমনা শিশুরা বিশ্বাস করে তাহাদের মাতা, পিতা বা গুরুজনের কথিত জ্বীন-পরী, ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব ইত্যাদি সম্বন্ধে কল্পিত কাহিনীগুলি এবং নানাবিধ রূপকথা, উপকথা ও অতিকথা। শিশুমনে ঐগুলি এমনই গভীরভাবে দাগ কাটে যে, বার্ধক্যেও অনেকের মন হইতে উহা বিলীন হইতে চাহে না। এই জাতীয় বিশ্বাস অর্থাৎ যে সমস্ত কাহিনীর বিষয়সমূহে ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনো প্রমাণ নাই অথবা কার্যকারণ সম্বন্ধ ব্যাখ্যা করার কোনো প্রয়াস নাই, এক কথায় যুক্তি যেখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত, এইরূপ কাহিনীতে বিশ্বাস রাখার নামই অন্ধবিশ্বাস। অনুরূপভাবে মানুষের জাতিগত জীবনের বাল্যকালে তৎকালীন মোড়ল বা সমাজপতিগণ নানাবিধ হিতোপদেশের সহিত বহু রূপকথা, উপকথা ও অতিকথা যুক্ত করিয়া পরিবেশন করিয়াছিলেন এবং সাধারণ মানুষ তাহা তৃপ্তিসহকারে গলাধঃকরণ করিয়াছিল এবং উহার ফলে মানুষের জীবন। হইয়াছিল অসুস্থ ও বিকারগ্রস্ত। আর উহা কৌলিক ব্যাধির ন্যায় বংশপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া। এইরূপ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অন্ধবিশ্বাসকে বলা হয় কুসংস্কার। দুঃখের বিষয়, মানুষের জাতিগত জীবনের যৌবনে বিংশ শতাব্দীর এই বিজ্ঞানের যুগেও বহু লোক অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের গভীর সমুদ্রে ডুবিয়া রহিয়াছে।
মানব সমাজে কুসংস্কারের বীজ উপ্ত হইয়াছিল হাজার হাজার বৎসর পূর্বে। এখন উহা প্রকাণ্ড মহীরূহের আকার ধারণপূর্বক অসংখ্য শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া এবং ফুলে-ফলে সুশোভিত হইয়া বিস্তীর্ণ জনপদ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। আর তাহারই ছায়াতলে কালাতিপাত করিতেছে লক্ষ লক্ষ মানুষ।
অতীতে বহু মনীষী কুসংস্কাররূপী মহীরূহের মূলে যুক্তিবাদের কুঠারাঘাত করিয়া গিয়াছেন, যাহার ফলে বহু মানুষ উহার ছায়াতল হইতে বাহির হইয়া দাঁড়াইয়াছে মুক্তমনের খোলা মাঠে আর তরুণ-তরুণীরা ভিড় জমাইতেছে দর্শন-বিজ্ঞানের পুস্পোদ্যানে।
এই পুস্তকখানির আদান্ত অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিলে সুধী পাঠকবৃন্দ বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে মানবমনের ধারাবাহিক চিন্তা, গবেষণা ও সর্বশেষ যুক্তিসম্মত মতবাদের বিষয় জানিতে পারিবেন।
এই পুস্তকখানি প্রণয়নে প্রণেতা হিসাবে তত্ত্বমূলক অবদান আমার কিছুই নাই। তত্ত্ব যাহা পরিবেশিত হইয়াছে তাহা সমস্তই সংকলন, আমি উহার সংগ্রাহক মাত্র। ইহা প্রণয়নে আমি যে সমস্ত গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি, তাহার গ্রন্থকারগণের নিকট আমি চিরঋণে আবদ্ধ।
এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপিখানা বরিশালের সরকারি ব্রজমোহন মহাবিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় কাজী গোলাম কাদির সাহেব ও মাননীয় অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল হক সাহেব তাহাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়া পরম ধৈর্যসহকারে পাঠ করিয়া উহা সংশোধনের প্রয়াস পাইয়াছেন এবং ইহার প্রুফ সংশোধনে সহায়তা করিয়াছেন মাননীয় অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল ইসলাম সাহেব। বাংলা একডেমীর প্রাক্তন মহাপরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজি বিভাগের চেয়ারম্যান মাননীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী সাহেব দয়াপরবশ হইয়া পাণ্ডুলিপিখানা পাঠ করিয়া কতিপয় ভ্রম সংশোধনের ইঙ্গিত দান করিয়াছেন। বিশেষত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রবীণ অধ্যাপক ও আবুজর গিফারী কলেজ (ঢাকা)-এর অধ্যক্ষ জনাব দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ তাহার নানারূপ অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এই পুস্তকখানার ভূমিকা লিখিয়া ইহার মর্যাদাবৃদ্ধি করিয়াছেন। এই সমস্ত বিদগ্ধজনের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।
এই পুস্তকখানার রচনাকাল ১৯. ৪. ১৩৭২ হইতে ২৫. ৪. ১৩৭৭, কিন্তু মুদ্রণকাল মাঘ, ১৩৮৪। এই সময়ের মধ্যে দেশ তথা সমাজে নানারূপ উত্থান-পতন ও ভাগা-গড়া ঘটিয়াছে আর বিজ্ঞান জগতে নানাবিধ পরিবর্তন ঘটিয়াছে বিজ্ঞানীদের নব নব আবিষ্কারের ফলে। তাহারই পরিপ্রেক্ষিতে আবশ্যক হইয়াছিল এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপিখানার কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের। আর সেই সংশোধনের বিরক্তিকর ঝামেলার বেশির ভাগই ভোগ করিতে হইয়াছে। প্রেস কর্তৃপক্ষকে। ইহাতে প্রেস কর্তৃপক্ষ মো. তাজুল ইসলাম সাহেব ও তাহার কর্মচারীবৃন্দের উদারতা ও সহিষ্ণুতা আমাকে বিমুগ্ধ করিয়াছে।
নানা কারণে এই পুস্তকখানিতে এমন কতগুলি ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকিয়া গেল, যাহা শুদ্ধিপত্র দ্বারাও দূর করা দুষ্কর। ইহার জন্য প্রিয় পাঠকবৃন্দের নিকট আমার ক্ষমা প্রার্থনা ভিন্ন আর কোনো উপায় নাই।
বিনীত
আরজ আলী মাতুব্বর
লামচরি
১১ আষাঢ় ১৩৮৪
০১. আদিম মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব
চৈনিক মত
প্রাচীন চীনাদের বিশ্বাস, তাহারা চীন দেশেরই আদিম অধিবাসী। তাহারা যে অন্য কোনো দেশ হইতে সেখানে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে, তাহাদের কোনো পুরাণ-গ্রন্থাদিতে এই কথা নেই। চীন দেশে ঈশ্বর প্রথম যে মনুষ্যটি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার নাম ‘পাং-কু’। পাং-কুর উৎপত্তি দশ লক্ষ বৎসর পরে চীনে দশটি রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছিল। প্রথম দেবগণের রাজত্ব, দ্বিতীয় উপদেবগণের রাজত্ব, তৃতীয় নরগণের রাজত্ব, চতুর্থ জুচানগণের রাজত্ব, পঞ্চম সুইজন বা অগ্ন্যুৎপাদকগণের রাজত্ব ইত্যাদি। ইতিহাসে চীনের প্রথম রাজার নাম ‘ফু-হিয়া’। ইঁহার রাজত্বকাল (পাশ্চাত্য মতে) ২৮৩২-২৩৩৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে। ইহাই চীনের সৃষ্টি প্রকরণের প্রাচীন বিবরণ।
মিশরীয় মত
মিশরের কোনো কোনো প্রদেশের প্রাচীন অধিবাসীগণের বিশ্বাস, সৃষ্টিকর্তা ‘ক্ষুণুম’ প্রথমে ডিম্বাকার পৃথিবী এবং পরে মনুষ্য সৃষ্টি করেন। অন্যত্র আবার প্রচার, শিল্পনিপুণ ঈশ্বর ‘টা’ নামক হাতুড়ি দ্বারা পূর্বোক্ত ডিম্ব ভাঙ্গিয়া ফেলেন, সেই ডিমের মধ্য হইতে পৃথিবী ও প্রাণীগণের উৎপত্তি হয়। কাহারও কাহারও মতে ‘থোথ’ বা চন্দ্রদেবতার আদেশক্রমে পৃথিবী উত্থিত হয়। অনেকের মতে ‘রা’ বা ‘রে’ (সূর্যদেবতা) পৃথিব্যাদি সকলের সৃষ্টিকর্তা।
অন্যমতে—মিশরের প্রথম রাজার নাম ‘রা’ বা ‘রে’। মনুষ্যগণ তাঁহার সম্মান করে নাই বলিয়ে বৃদ্ধবয়সে তিনি বড়ই রুষ্ট হন। প্রথমে তিনি মনুষ্য সমাজকে ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিপক হইয়াছিলেন। পরিশেষে স্বর্গীয় গাড়িতে আরোহণ করিয়া এক নুতন পৃথিবী সৃষ্টি করেন। তাঁহার সেই পৃথিবীর নামই ‘স্বর্গ’।
ফিনিসীয় মত
ফিনিসিয়ার অধিবাসীদিগের বিশ্বাস, ক্রন্স্ নামক দেবতা ফিনিসিয়া ও তাহার অধিবাসীদিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সৃষ্টিকর্তা ক্রন্স্-এর পশ্চাতে ও সম্মুখে দুইদিকেই চক্ষু ছিল। তাহার ছয়টি পক্ষ, তন্মধ্যে কয়েকটি বিস্তারিত ও কয়েকটি সঙ্কুচিত। প্রাচীন ফিনিসীয়দের মতে ক্রন্স্ই এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টিকর্তা।
ব্যাবিলনীয় মত
প্রাচীন ব্যাবিলনীয়দের মত এই—প্রথমে সংসার জলময় ছিল। ‘অপসু’ ও ‘তিয়ামত’ দেবতাগণ উৎপন্ন হন। সেই সকল দেবতা তিয়ামতের সন্তান-সন্ততির মধ্যে পরিগণিত। এক সময় তিয়ামতের সহিত দেবগণের বিরোধ উপস্থিত হয়। তখন ‘মার্দক’ বা ‘মেরোডাক’ (ঈশ্বর) দেবতাগণের অধিপতি ছিলেন। তিনি তিয়ামতের সংহার সাধন করেন। তিয়ামত আপনার সহায়তার জন্য যে দৈত্যসমূহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, মার্দক তাহাদিগকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখেন। অবশেষে মার্দক কর্তৃক তিয়ামতের দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়। সেই দেহের একাংশে পৃথিবী এবং অপর অংশে স্বর্গ সৃষ্ট হইয়াছিল।
আফ্রিকার অসভ্য জাতিদের মত
আফ্রিকা মহাদেশের বন্য জাতিদিগের মধ্যে সৃষ্টি সম্বন্ধে একটা সাধারণ উপাখ্যান প্রচলিত আছে। এক সম্প্রদায়ের লোকের বিশ্বাস, ‘মাণ্টিস’ জাতীয় পতঙ্গই সৃষ্টির আদিভূত। মাণ্টিস জাতীয় পতঙ্গের মধ্যে ‘ফাগন’ বা ‘ইকাগন’ পতঙ্গ পরম উপকারী বলিয়া পূজিত হইয়া থাকে (দেব-দেবীর সহচর বলিয়া এদেশের হিন্দুদের নিকট সর্প, বৃষ, পেঁচক, মূষিক ইত্যাদিও সম্মানার্হ বা পূজনীয়)। তাহাদের বিশ্বাস—মণ্টিসের স্ত্রী, কন্যা ও দৌহিত্র আছে। মাণ্টিস আপন জামাতার পাদুকা হইতে দ্বীপের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাহার নিজের পাদুকা হইতে চন্দ্র উৎপন্ন হয়। চন্দ্রের বর্ণ রক্তিমাভ দেখিয়া উক্ত বন্য জাতিরা সিদ্ধান্ত করে, মাণ্টিসের পাদুকায় রক্তবর্ণ ধূলা ছিল বলিয়া চন্দ্রের এইরূপ বর্ণ হইয়া থাকিবে। একটি বিড়ালের সহিত যুদ্ধে একবার মাণ্টিস পরাজিত হয়। যাহা হউক, ঐ সকল জাতি মাণ্টিসকেই ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করে।
দক্ষিণ আফ্রিকার হটেনটট জাতির মতে, সৃষ্টিকর্তা নাম ‘সুনিগোয়ান’। তাহার উপাসনগণ বলিয়া থাকেন, তিনিই অবিদ্যমান শূন্য হইতে বিশ্বের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।
দক্ষিণ আফ্রিকার জুলু জাতি প্রধানত পিতৃপুরুষের উপাসক। তাহাদের মতে, পিতৃপুরুষগণের এক আদিপুরুষই এই সসাগরা ধরিত্রীর সৃষ্টিকর্তা। জুলুরা বলে, সেই আদিপুরুষ বা সৃষ্টিকর্তাই পৃথিবীর আদিমানুষ। তাহার নাম ‘উনকুলুলু’। তাহা হইতেই অন্যান্য সবকিছুর সৃষ্টি হইয়াছে।
অস্ট্রেলিয়ার আদিম জাতির মত
অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের অন্তর্গত ভিক্টোরিয়া প্রদেশের উত্তরাংশে যে সকল আদিম অধিবাসী বাস করে, তাহারা বলে, পণ্ডজিল নামক পক্ষীই এই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা। সেই পক্ষীই পৃথিবীকে খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত করিয়াছে।
অস্ট্রেলিয়ার অন্যান্য অংশের আদিম অধিবাসীদিগের বিশ্বাস, ‘নুরালি’ অর্থাৎ অতি প্রাচীনকালের মনুষ্যগণই এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।
আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের মত
আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সৃষ্টিবর্ণনায় অস্ট্রেলিয়ান মতেরই ছায়াপাত হইয়াছে। কোথায়ও পক্ষী হইতে, কোথায়ও বা বিশেষ বিশেষ জন্তু হইতে এই পৃথিবী ও প্রাণীসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া প্রচারিত রহিয়াছে।
উত্তর আমেরিকার আলাস্কা প্রদেশে সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার অভিব্যক্তিমূলক একটি প্রতিমূর্তি দৃষ্ট হয়। ঐ মূর্তিটি এক্ষণে পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তভূর্ত যাদুঘরে রক্ষিত আছে। ঐ অঙ্কিত প্রতিচিত্রে একটি কৃষ্ণবর্ণ কাক মানুষের মুখোশের উপর বসিয়া আছে। বোধ হইতেছে যেন কাকটি তা দিয়া তা দিয়া ডিম্ব হইতে মনুষ্য সৃষ্টি করিতেছে। এই চিত্রটি দর্শনে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, ডিম্ব হইতেই জীবসমাকুল পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে, ইহাই আলাস্কাবাসীদের মত।
সৃষ্টি সম্বন্ধে আমেরিকান রেড ইণ্ডিয়ান জাতিদিগেরও ঐরূপ বিশ্বাস। উত্তর-পশ্চিম তীরের থিলিঙ্কিট ইণ্ডিয়ান নামক অধিবাসীগণ কতকাংশে উক্ত মতেরই পোষকতা করিয়া থাকে। তাহাদের মতে, ‘জেল’ বা ‘জেল্চ্’ অর্থাৎ দাঁড়কাক আপনিই উদ্ভূত হয়। সেই দাঁড়কাকই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা। ঐ দাঁড়কাক একটি বাক্স হইতে চন্দ্র, সূর্য এবং নক্ষত্রসমূহকে বাহির করিয়া অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবীতে আলোকরশ্মি আনয়ন করিয়াছিল।
উত্তর আমেরিকার আল্গকিন জাতির মধ্যে সৃষ্টিবিষয়ক প্রচলিত মত—‘মিকাবো’ অর্থাৎ এক বৃহৎ খরগোশ কর্তৃক পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছিল। সেই খরগোশ ভেলার সাহায্যে অন্যান্য জন্তুকে রক্ষা করিয়াছিল। ভেলায় অবস্থিত জন্তুর মধ্যে তিনটিকে খরগোশরাজ একে একে সমুদ্রের তলদেশে মাটি আনিবার জন্য প্ররণ করে। সমুদ্রতল হইতে তাহারা অল্প বালুকণা লইয়া আসে। সেই বালুকণা হইতে খরগোশরাজ একটি দ্বীপের সৃষ্টি করে। সেই দ্বীপটিই এই পৃথিবী। মৃত জন্তুসমূহের অস্থি-কঙ্কাল লইয়া খরগোশরাজ মনুষ্যের সৃষ্টি করিল। ঐ জাতির মধ্যে জলপ্লাবন, প্রলয়, পুনঃ সৃষ্টি প্রভৃতির বিষয়ও বর্ণিত আছে।
উত্তর আমেরিকার ইরোকো নামক সম্প্রদায় আবার অন্য মত পোষণ করে। তাহারা বলে, উপরে স্বর্গ ও নিম্নে অনন্ত বারিধি ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। স্বর্গের একটি ছিদ্রের মধ্য দিয়া একটা আতোয়ান্ত্রিসিক নাম্নী এক রমণী জলমধ্যে নিপতিত হয়। সেই স্থানে একটি কচ্ছপ ছিল। কোনো একটি জলজন্তু কর্তৃক কচ্ছপের পৃষ্ঠদেশে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা রক্ষিত হইয়াছিল। রমণী স্বর্গ হইতে সেই কচ্ছপের পৃষ্ঠে পতিত হয় (আতোয়ান্ত্রিসিক ও বিবি হাওয়ার ভূপতনের আখ্যানে কিছুটা সাদৃশ্য আছে)। রমণী ঐ সময় গর্ভবতী ছিল। তাহার গর্ভ হইতে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। সেই কন্যা হইতে যমজ পুত্রদ্বয় উৎপন্ন হয়। তাহাদের নাম জোস্কেহা ও টাওয়াস্কারা। জোস্কেহার সহিত বিরোধ হওয়ায় টাওয়াস্কারা আবার মাতাকে নিহত করে। তাহাদের মাতার কঙ্কাল হইতে উদ্ভিদাদি উৎপন্ন হয়। জোস্কেহা মানুষ ও পশু সৃষ্টি করে।
মেক্সিকোর অধিবাসীগণ সৃষ্টির পাঁচটি পর্যায় স্বীকার করে। প্রথম চারিটি পর্যায়ের নাম—স্থল, অগ্নি, বায়ু ও জল (এই মতটি গ্রীক দার্শনিক এম্পিডোকল্স-এর মতের অনুরূপ; তাঁহার মতে সৃষ্টির মৌলিক উপাদান ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও মরুৎ–অর্থাৎ আব, আতস, খাক, বাত)। পঞ্চমটির নাম নির্দিষ্ট হয় নাই (ভারতীয় আর্যদের মত অনুসারে অতিরিক্তটি ‘পঞ্চভূত’-এর অন্তর্গত ‘ব্যোম’ বলিয়া মনে হয়; ব্যোম অর্থ আকাশ বা শূন্য)। তাহাদের মতে, প্রথম যুগে মৃত্তিকার সৃষ্টি অগ্নি অথবা তাপ বা আলোকপুঞ্জ, তৃতীয় বায়ব পদার্থ, চতুর্থ জলীয় বা বাষ্পীয় পদার্থ। মেক্সিকোবাসীগণ জলপ্লাবনে বিশ্বাসবান।
মেক্সিকোবাসীদের সৃষ্টি প্রকরণে পাশ্চাত্যের বেশ কিছুটা ছাপ আছে।
পেরুদেশবাসীরা তিনজন সৃষ্টিকর্তার প্রাধান্য স্বীকার করিয়া থাকে। তাহাদের—১. ‘পাচা কামাক’, উনি ভূগর্ভস্থ অগ্নিদেবতা; ২. ‘ভিরা কোচা’, ইনি পৃথিবীর সৃষ্টি ও গঠনকর্তা বলিয়া পূজিত; ৩. ‘মাংকোকাপাক; বা অদ্বিতীয় মনুষ্য, তাঁহার পত্মী ও ভগ্নী ‘সৃষ্টিকারী ডিম্ব’ নামে অভিহিত। অদ্বিতীয় মনুষ্য ও ডিম্ব পরিশেষে সূর্য ও চন্দ্র রূপে প্রকাশমান হন। যুকাসদিগের পুরোহিতগণ তাঁহাদিগকে রাজা ও রাণী নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।
ব্রাজিলের কোনো কোনো জাতি বলিয়া থাকে, জামোয়া নামক দেবতা পৃথিবীর প্রথম মনুষ্যের পিতামহ। তাহার দ্বারাই সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন হয়। উত্তর আমেরিকার এস্কিমো জাতি বলিয়া থাকে, এই পৃথিবী অনন্তকাল বিদ্যমান আছে। কোনো দিন কেহ ইহাকে সৃষ্টি করে নাই।
আমেরিকার অধিকাংশ জাতি সূর্যদেবকে সৃষ্টিকর্তা ও পরমেশ্বর বলিয়া মান্য করে। কিন্তু এস্কিমোগণ এবং উত্তর আমেরিকার আথাবাস্কা জাতি সূর্যদেবের প্রাধান্য আদৌ স্বীকার করে না। এতদপ্রসঙ্গে জার্মান পণ্ডিত অধ্যাপক রাজেল একটি অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলেন, এস্কিমো প্রভৃতি জাতির বাসস্থান উত্তর আমেরিকায়। চির তুষারাবৃত পৃথিবীর ঐ অংশে মনুষ্যগণ মাংসাদি খাইয়াই জীবন ধারণ করে। সূর্যের সহিত তাহাদের সম্বন্ধ অতি অল্প। সুতরাং তাহারা সূর্যের প্রাধান্য স্বীকার করে না। তিনি আরও বলেন, পৃথিবীর যে যে অংশে চাষাবাদ নাই, সেখানকার লোকেরা কদাচ সূর্যের উপাসনা করে না।
পলিনেশীয়দের মত
পলিনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সৃষ্টি সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। স্যার জর্জ গ্রে পলিনেশিয়ার পৌরাণিক বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এবং অন্যান্য গ্রন্থকারগণের বর্ণনায় প্রকাশ, পলিনেশিয়ার মাওয়ারী জাতির বিশ্বাস—‘রাঙ্গী’ ও ‘পাপা’ অর্থাৎ স্বর্গ ও পৃথিবী প্রথমে একত্রে সংযুক্ত ছিল। সহসা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ায় স্বর্গ উপরে চলিয়া যায়, পৃথিবী নিম্নে পড়িয়া থাকে (‘স্বর্গ উপরদিকে’—এই মতটি ধর্মজগতের বহুক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থিত)। মাওয়ারীগণ বলে, রাঙ্গী ও পাপার পুত্রের নাম তাঙ্গালোয়া বা তারোয়া। তিনি জনদেবতা, সমুদ্রের অধিপতি। তিনি মৎস্য ও সরীসৃপকূল সৃষ্টি করেন। পলিনেশিয়ার অন্যান্য অংশের অধিবাসীরা আবার তাঙ্গালোয়াকেই অদ্বিতীয় পরমেশ্বর বলিয়া স্বীকার করে। তাহাদের মতে, তিনিই সৃষ্টিকর্তা। শ্যামোয়া দ্বীপে তাহার নাম তাঙ্গালোয়ালাঙ্গী। তাঙ্গালোয়া ও লাঙ্গী এই উভয় শব্দেই স্বর্গকে বুঝাইয়া থাকে। মেঘমণ্ডলকে তাহারা তাঙ্গালোয়ার পোত বা তরণী বলিয়া বিশ্বাস করে। কখনও কখনও তাঙ্গালোয়া শম্বুকের মধ্যে বাস করেন বলিয়া প্রবাদ আছে। সময় সময় তাঙ্গালোয়া আপনার অধিষ্ঠানভূত শম্বুকটিকে পরিত্যাগ করিতেন, তদ্বারা পৃথিবীর অবয়ব ও প্রাণীসংখ্যা বৃদ্ধি পাইত। আবার কোনো কোনো স্থানে প্রচার, তাঙ্গালোয়া ডিম্বের মধ্যে বাস করিতেন, তদ্বারা দ্বীপসমূহের উৎপত্তি হইত।
পলিনেশিয়ায় তাঙ্গালোয়া সম্বন্ধে আর একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে—অতি প্রাচীনকালে তাঙ্গালোয়া এক বৃহদকার পক্ষীরূপে সমুদ্রের উপর বিচরণ করিতেন। সেই সময় তিনি জলের উপর একটি ডিম্ব রক্ষা করেন। সেই ডিম্বই পৃথিবী ও স্বর্গ অথবা সূর্য।
নিউজিল্যাণ্ড দ্বীপের অধিবাসীরা তাঙ্গালোয়ার প্রাধান্য স্বীকার করে না। তাহাদের মতে, ‘মানি’ অদ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা ও পরমেশ্বর। তিনি প্রথমে বায়ু ও বন্যা সৃষ্টি করেন। তাহা হইতে অন্যান্য পদার্থ উদ্ভূত হয়। দেবগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে পলিনেশিয়াবাসীগণ সাধারণত বলিয়া থাকে যে ‘পো’ হইতে দেবগণের উদ্ভব হইয়াছে। ‘পো’ শব্দে অন্ধকার বুঝায়। সে হিসাবে অন্ধকারই সকলের জনয়িতা। এমনকি তাঙ্গালোয়া পর্যন্ত অন্ধকার হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন।(১)
————————-
১. রচনা সংগ্রহ – রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী
০২. ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্ব
ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্ব
# বৈদিক ধর্ম
বেদ-বিধানাত্মক ধর্মই বৈদিক ধর্ম। বৈদিক ধর্মের বর্তমান নাম হিন্দুধর্ম। বেদ চারিখানা। যথা –ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব। বেদ রচিত হইবার বহু পরে উহার ভাষ্য-অনুভাষ্য, টীকা ইত্যাদি এবং পুরাণ, উপপুরাণ, গীতা, তন্ত্র ইত্যাদি অজস্র শাস্ত্রগ্রন্থ রচিত হইয়া উহা বৈদিক ধর্মে গৃহীত হইয়াছে। সেই সবের মধ্যে কয়েকখানা গ্রন্থের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় মতবাদ এইখানে আলোচিত হইল।
ঋগ্বেদ (পুরুষ সুক্ত) – “পুরুষ (ঈশ্বর) সহস্র মস্তকযুক্ত এবং সহস্র অক্ষি ও সহস্র পদ বিশিষ্ট। তিনি বিশ্বচরাচর সর্বত্র পরিব্যাপ্ত ও দশদিকে বিরাজমান (১)। যাহা উৎপন্ন হইয়াছে, যাহা উৎপন্ন হইবে, সকলই সেই পুরুষ। তিনি অমরত্বের অধিকারী। তিনি অন্নের (ভাতের) দ্বারা পরিপুষ্ট (২)। সেই পুরুষের মহিমার অন্ত নাই। তাহার এক পদে ভূতসমষ্টিপূর্ণ এই পৃথিবী এবং অপর তিন পদে অমরগণ পরিপূরিত স্বর্গ (৩)। তিনি চেতন, অচেতন সকল সামগ্রীতেই পরিব্যাপ্ত। তাহা হইতেই বিরাট জন্মগ্রহণ করেন। বিরাট হইতে আবার পুরুষ উৎপন্ন হ’ন (৪)। তিনি জন্মমাত্র অগ্রপশ্চাতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন; সেই পুরুষকেই হব্যরূপে গ্রহণ করিয়া দেবতারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তখন বসন্ত ঘৃত হইয়াছিল, গ্রীষ্ম যজ্ঞকাষ্ঠ এবং শরৎ হবি হইয়াছিল (৫)। সেই যজ্ঞাগ্নি হইতে জল এবং খেচর ও ভূচর, আরণ্য ও গ্রাম্য পশু উৎপন্ন হইল (৬)। সেই যজ্ঞ হইতে ঋক, সাম উৎপন্ন হইল; ছন্দসকল আবির্ভূত হইল; যজু উৎপন্ন হইল (৭)। তাহা হইতে অশ্ব উৎপন্ন হইল এবং দুই পাটি দন্তযুক্ত পশুগণ জন্মগ্রহণ করিল। তাহা হইতে গো-গণ জন্মগ্রহণ করিল, তাহা হইতে ছাগ ও মেষ উৎপন্ন হইল (৮)। সেই পুরুষ বিভক্ত হইলে … তাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং পদদ্বয় হইতে শূদ্রের উৎপত্তি হয় (৯)। তাহার মন হইতে চন্দ্র, চক্ষু হইতে সূর্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি এবং প্রাণ হইতে বায়ু বা জীবের প্রাণবায়ু উৎপন্ন হইয়াছিল (১০)। তাহার নাভি হইতে অন্তরীক্ষ, মস্তক হইতে স্বর্গ, চরণদ্বয় হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিকসকল ও লোকসমূহ উৎপন্ন হয় (১১)।” ইত্যাদি।
শতপথ ব্রাহ্মণ (৬/১/১) –“পুরুষ প্রজাপতি প্রথমে জলের সৃষ্টি করিয়া জলমধ্যে আপনি অণ্ডরূপে প্রবিষ্ট হন। সেই অণ্ড হইতে জন্মগ্রহণ করিবার জন্যই তিনি তাহাতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি তাহা হইতে ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকারী ব্রহ্মরূপে আবির্ভূত হন।”
অথর্ব সংহিতা (১১/৪) — “প্রাণ হইতেই অর্থাৎ প্রাণস্বরূপ পরমেশ্বর হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি হয়, পরমেশ্বর স্বয়ংই প্রথমসৃষ্টরূপে আবির্ভূত হন।”
তৈত্তিরীয় উপনিষদ (২/৬) –“ব্ৰহ্ম ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব, বহুরূপে প্রকাশমান হইব। অতঃপর তিনি তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। সেই তপস্যার ফলে পরিদৃশ্যমান বিশ্বের সৃষ্টি হয়। বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া তিনি স্বয়ং তাহার মধ্যে প্রবেশ করেন এবং সর্বরূপে আবির্ভূত হন।”
ঐতরেয় উপনিষদ (১/১-২; ১/৩/১১) — “সষ্টির আদিতে একমাত্র আত্মাই বিদ্যমান ছিলেন, তিনি ভিন্ন আর কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। তিনি সংকল্প করেন, আমি জগত সৃষ্টি করিব। তদনুসারে তিনি ভূলোক, দ্যুলোক, রসাতল, সমুদ, আকাশ, মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি সৃষ্টি করেন। … তখন তিনি চিন্তা করেন, কি করিয়া উহার মধ্যে প্রবেশ করিবেন। এইরূপ চিন্তার পর তিনি শীর্ষ বিদীর্ণ করিয়া সকলের মধ্যে প্রবেশ করেন।”
মনু সংহিতা (১; ৬) –“প্রলয়ান্তে বহিরিন্দ্রিয়ের অগোচর অব্যাহত সৃষ্টিসামর্থ সম্পন্ন ও প্রকৃতি প্রেরক পরমেশ্বর স্বেচ্ছাকৃত দেহধারী হইয়া এই আকাশাদি, পঞ্চভূত ও মহদাদি তত্ত্ব, যাহা প্রলয়কালে সূক্ষরূপে অব্যক্তাবস্থায় ছিল, সেই সমুদয় স্থলরূপে প্রকাশকরত আপনিই প্রকাশিত হইলেন।”
এই বর্ণনাটি আধুনিক নীহারিকাবাদ-এর সহিত বহুলাংশে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
মনু (১; ৮) –“সেই পরমাত্মা প্রকৃতিরূপে পরিণত আপন শরীর হইতে নানা প্রকার প্রজা সৃষ্টি করিবার অভিলাষে, কিরূপে সৃষ্টি সম্পাদন হইবে, এই সঙ্কল্প করিয়া, প্রথমত ‘জল হউক’ বলিয়া আকাশাদিক্রমে জলের সৃষ্টি করিলেন ও তাহাতে আপন শক্তিরূপ বীজ অর্পণ করিলেন।”
মনু (১; ৯)— “অর্পিত বীজ সুবর্ণনির্মিতের ন্যায় ও সূর্যসদৃশ প্রভাযুক্ত একটি অণ্ড হইল। ঐ অণ্ডে সকল লোকের জনক স্বয়ং ব্রহ্মই শরীর পরিগ্রহ করিলেন।”
এইখানে বলা হইতেছে যে, জলে অর্পিত শক্তির বীজ হইতে সুবর্ণের ন্যায় বর্ণ ও সূর্যের ন্যায় প্রভাযুক্ত একটি ডিম্বাকার পদার্থের সৃষ্টি হইল, যাহার অভ্যন্তরে নিহিত থাকিলেন সকল সৃষ্টির জনক স্বয়ং ব্রহ্মা। ব্রহ্ম’ মানে তেজ বা অগ্নি। ইহাতে মনে হয় যে, উক্ত ডিম্বটি সূর্য ভিন্ন আর কিছুই নহে। বর্তমানে প্রমাণিত হইয়াছে যে, সূর্য একটি অগ্নিপিণ্ড এবং গ্রহাদির জনক ও পৃথিবীস্থিত জৈবাজৈব যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু জল হইতে সূর্যের উৎপত্তি সম্ভব নহে।
মনু (১; ১২)– “ভগবান ব্রহ্মা সেই অণ্ডে ব্রাহ্ম পরিমাণে এক বৎসরকাল বাস করিয়া, ‘ দ্বিধা হউক’ মনে হইবামাত্র সেই অণ্ডকে দুই খণ্ড করিলেন।”
সেই ব্রহ্ম-অণ্ডটি (সূর্য) খণ্ডিত হইয়া পৃথিবীর জন্ম হইয়াছে –ইহা আধুনিক বিজ্ঞানীগণও বলেন, কিন্তু দুই খণ্ড বলেন না, বলেন দ্বাদশ খণ্ড। যথা –বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো, ভালকান, পসিডন ও স্বয়ং রবিদেব। আর রবিদেব তাহার এক বৎসর বয়সের সময়ে খণ্ডিত হয় নাই, হইয়াছে কোটি কোটি বৎসর বয়সের সময়ে।
মনু (১; ১৩)– “তিনি দুই খণ্ডের উৰ্ব খণ্ডে স্বর্গ ও অপর খণ্ডে পৃথিবী করিলেন” (কোনো কোনো অসভ্য জাতিও এই মতটি পোষণ করে) এবং মধ্যভাগে আকাশ, অষ্ট দিক ও চিরস্থায়ী সমুদ্র নামক জলাধার প্রস্তুত করিলেন। ব্রহ্ম-অণ্ডটি দুই খণ্ড হইয়া এক খণ্ডে স্বর্গ ও অপর খণ্ডে পৃথিবীর সৃষ্টি হইল এবং মধ্যস্থানটিতে সৃষ্টি হইল আকাশ, অষ্টদিক ও সমুদ্রের। ইহাতে বুঝা যায় যে, সমুদ্র পৃথিবীতে অবস্থিত নহে, উহা শূন্যে অবস্থিত।
মনু (১; ১৫) –“আর সত্ত্ব, রজস্তমো গুণযুক্ত অন্য পদার্থসকল সৃষ্টি করিলেন এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধের গ্রাহক শ্রোত্র, ত্বক, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা — এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাক, পাদ, হস্ত, গুহ্য, উপস্থ –এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় সৃষ্টি করিলেন।”
এইখানে দেখা যায় যে, জীবসৃষ্টির পূর্বেই তাহার ইন্দ্রিয়সকল সৃষ্ট হইয়াছে।
মনু (১; ৩২) — “সৃষ্টিকর্তা জগদীশ্বর আপন শরীরকে দুই খণ্ড করিয়া অর্ধাংশ পুরুষ ও অর্ধাংশ নারী হইলেন। ঐ উভয়ের পরস্পর সংযোগে বিরাট নামক পুরুষ উৎপন্ন হইল।”
মনু (১; ৩৩) –“হে দ্বিজসত্তম! সেই বিরাট পুরুষ বহুকাল তপস্যা করিয়া যাহাকে সৃষ্টি করিলেন, আমি সেই মনু। আমাকে সৃষ্টিকর্তা বলিয়া অবগত হও।”
জগদীশ্বরের পুত্র বিরাট জন্মিলেন জগদীশ্বরীর গর্ভে এবং বিরাটের পুত্র মনু জন্মিলেন তাঁহার স্ত্রীর গর্ভে নহে, তপস্যার বলে। মনু সম্পর্কে হন জগদীশ্বরের পৌত্র (নাতি)। এই মনু হইতে উৎপত্তি হইয়াছে মনুষ্য বা মানব –এই নামটির।
মনু (১; ৩৪/৩৫) –“অনন্তর আমি (মনু) প্রজা সৃষ্টি করিবার অভিলাষে বহুকাল কঠোর তপস্যা করিয়া প্রথমে প্রজাসৃজনে সমর্থ দশজন প্রজাপতির সৃষ্টি করিলাম।”… যথা — “মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ।”
এইখানেও মনু দশজন প্রজা (পুত্র) জন্মাইলেন তপস্যার বলে, কোনো নারীর গর্ভে নহে। বিশেষত কন্যা একটিও জন্মাইলেন না।
মনু (১; ৩৬–৪১) — “মরীচ্যাদি দশ প্রজাপতি আবার সাতজন মনু (মনুষ্য) সৃষ্টি করিলেন এবং সৃষ্টি করিলেন যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, অসুর, মেঘ, বিদ্যুৎ, বজ, নক্ষত্র, ধূমকেতু, মানুষ, পশু, পাখি, সরীসৃপ-মৎস্যাদি জলজীব, উদ্ভিদ, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি।”
মরীচ্যাদি দশ প্রজাপতি আবার সাতজন মনু সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু এই সকল মনুরা প্রজাপতিদের ঔরসজাত, না হাতে গড়া, তাহার কোনো হদিস নাই। প্রতিমার মতো হাতে গড়া হইলে আবশ্যক ছিল উহাদের প্রাণ প্রতিষ্ঠার এবং ঔরসজাত হইলে আবশ্যক ছিল নারীর। কিন্তু কিছুরই উল্লেখ নাই।
.
আদি মনুর পৌত্র সপ্তমনুর মধ্যে কাহারও স্ত্রীর নামোল্লেখ নাই। অথচ তাহাদের বংশাবলীতে নাকি বর্তমান জগত মানুষে ভরপুর।
প্রজাপতিরাই নাকি সৃষ্টি করিয়াছেন একাধারে যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, অসুর ইত্যাদি এবং মানুষ, পশু, পাখি, বজ, নক্ষত্র ইত্যাদি সবই! পরেরগুলির অধিকাংশই পৃথিবীতে এখনও দেখা যায়। কিন্তু যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, অসুর ইত্যাদি গেল কোথায়?
মানুষ ও অন্যান্য জীবাদির জন্ম হইয়াছে নাকি প্রজাপতিদের ‘বংশে। কিন্তু মেঘ, বিদ্যুৎ, বজ্র, নক্ষত্র উহাদের বংশে জন্মিল কি রকম। বলা যাইতে পারে যে, প্রজাপতিরা জন্মদাতা নহেন, উহারা সৃষ্টিকর্তা। যদি তাহাই হয়, তবে সৃষ্টিকর্তা হন ব্রহ্মা, বিরাট পুরুষ, মনু ও দশ প্রজাপতি সমেত মোট তেরজন। চৌদ্দ ভুবনে চৌদ্দজন হওয়াই উচিত ছিল।
পৃথিবীতে নিত্য-নূতন জীবসৃষ্টি এখনও হইতেছে। কিন্তু প্রজাপতিরা কেহই বাঁচিয়া নাই। উহারা পরলোক গমনান্তে স্বর্গে বাস করিতেছেন। উত্তর আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল নামে যে। নক্ষত্রমণ্ডলটি আছে, উহা স্বর্গবাসী প্রজাপতিদেরই মণ্ডল। ওইখানেই নাকি নক্ষত্রের আকারে। সাতজন প্রজাপতি বাস করিতেছেন। যথা –মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ এবং তাঁহার স্ত্রী অরুন্ধতীও। কিন্তু উহারা বর্তমান দুনিয়ায় জীবাদি সৃষ্টির প্রতি আদৌ মনোযোগী নহেন। রাত্রিকালে মিটিমিটি চাহিতেছেন মাত্র।
.
# পার্সি ধর্ম
ইরান দেশের পার্সি ধর্মের প্রবর্তক জোরওয়াস্টার এবং প্রধান ধর্মগ্রন্থের নাম জেন্দ-আভেস্তা। ঐ ধর্মে সৃষ্টিকর্তার নাম অহুর-মজদা। জেন্দ-আভেস্তার মতে, অহুর-মজদার ইচ্ছাক্রমে পৃথিবী ও মনুষ্যাদি প্রাণীকুলের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু জেন্দ-আভেস্তার অংশবিশেষে দুইজন সৃষ্টিকর্তার আভাস পাওয়া যায়।
শেষোক্ত মতে– সৎপদার্থের বা সদগুণসমূহের সৃষ্টিকর্তা একজন এবং অসৎপদার্থ বা অসদগুণের সৃষ্টিকর্তা অপর একজন। সংসারে যত কিছু সৎসামগ্রী অর্থাৎ ভালো, তাহা সৃষ্টি করিয়াছেন অহুর-মজদা (আল্লাহ) এবং যত কিছু অসৎসামগ্রী বা মন্দ, তাহার সৃষ্টিকর্তার নাম আহরিমান (শয়তান)।
ইরানীয়গণের ধর্মগ্রন্থে প্রকাশ –ঐ দুই সৃষ্টিকর্তা আপন আপন স্বভাবের অনুরূপ প্রাণীসমূহ সৃষ্টি করেন। তিন সহস্র বৎসরকাল ঐ দুই সৃষ্টিকর্তার দুই রকম সৃষ্ট প্রাণী দুইটি কল্পরাজ্যে অবস্থিত ছিল। তৎপরে অসদাত্মা আহরিমান সদাত্মার সৃষ্ট প্রাণীর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। সেই বিবাদের ফলে উভয়ের মধ্যে সন্ধিশর্ত ধার্য হইয়াছিল। তাহাতে অহুর-মজদা নির্দেশ করিয়া দেন, সংসারে নয় হাজার বৎসর আহরিমানের প্রাধান্য থাকিবে, তন্মধ্যে তিন হাজার বৎসর তিনি সর্ববিষয়ে প্রাধান্য লাভ করিতে পারিবেন।
পারসিকদের ধর্মগ্রন্থে আরও লিখিত আছে– পবিত্ৰাত্ম অহুর-মজদা একটি বিশেষ মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক শেষোক্ত তিন হাজার বৎসর আহরিমানকে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলেন। সেই সময়ে অহুর-মজদা কর্তৃক স্বর্গীয় দূত (ফেরেশতা) সমূহ এবং পৃথিবী সৃষ্ট হয়। সেই সময়েই চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র প্রভৃতিকে অহুর-মজদা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহার পর আপনার সৃষ্ট দৈত্যগণ কর্তৃক উৎসাহিত হইয়া অসদাত্মা আহরিমান পুনরায় অহুর-মজদার সৃষ্ট পদার্থসমূহ ধংস করিতে বদ্ধপরিকর হয়। তখন অহুর-মজদার সৃষ্ট আকাশ, জল, পৃথিবী, গ্রহ-উপগ্রহ, প্রাণীসমূহের আদিভূত বৃষ এবং সৃষ্টির আদিমনুষ্য ‘গেওমাড’ প্রভৃতির সহিত দৈত্যগণের ঘোর যুদ্ধ চলিতে থাকে (শয়তানের দাগা)।
জেন্দ-আভেস্তার মতে– এই পৃথিবী ক্রমে ক্রমে ছয় বারে (দিনে) সৃষ্ট হইয়াছে (ইহা পবিত্র বাইবেল ও কোরানে অনুমোদিত)। প্রথম বারে আকাশ সৃষ্ট হইয়াছিল, দ্বিতীয় বারে জল, তৃতীয় বারে পৃথিবী, চতুর্থ বারে বৃক্ষাদি, পঞ্চম বারে প্রাণীসমূহ এবং ষষ্ঠ বারে গেওমাড নামক মনুষ্য (আদম?) সৃষ্ট হইয়াছিল।
.
# ইহুদি ও খ্রীস্টান ধর্ম
পবিত্র বাইবেল গ্রন্থখানা কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থের সমষ্টি এবং উহা দুই অংশে বিভক্ত। যাহারা প্রথম অংশ মানিয়া চলেন, তাহাদিগকে বলা হয় ইহুদি এবং যাহারা দ্বিতীয় অংশ মানিয়া চলেন, তাহাদিগকে বলা হয় খ্রীস্টান। কিন্তু প্রথমাংশের ‘আদিপুস্তক’ (Genesis) খানা ইহুদি ও খ্রীস্টান উভয় সম্প্রদায়ই মান্য করিয়া থাকেন এবং উভয় সম্প্রদায়ই সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে আদিপুস্তকখানার লিখিত বিবরণে বিশ্বাসী। কাজেই সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ মতামত একই। এইখানে সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে আদিপুস্তকে লিখিত বিবরণের আলোচনা করা যাইতেছে।
আদিপুস্তক (১; ১) –“আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন।”
সেকালের মানুষ তাহাদের সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিত যে, বিশালতায় আকাশ প্রথমস্থানীয় ও পৃথিবী দ্বিতীয়। তাই বলা হইত, প্রথম সৃষ্ট হইয়াছে আকাশ, পরে পৃথিবী। কেননা বৈদিক ও পারসিক গ্রন্থেও অগ্রে আকাশ সৃষ্টির বিবরণ পাওয়া যায় (মনু : ১; ৮)।
এককালে আকাশকে মনে করা হইত কোনো পদার্থের তৈয়ারী, পৃথিবীর উপরে বৃহৎ ঢাকনি। স্বরূপ। মনে করা হইত –চাঁদ, তারা, সূর্য আকাশের গায়ে লটকানো আছে এবং আকাশ হইতেই শিলা, বৃষ্টি, বজ্র ও তদূর্ধের স্বর্গ হইতে উল্কাপাত হইয়া থাকে। বস্তুত আমরা ঊর্ধ্বদেশে যে। নীলবর্ণের দৃশ্যটি দেখিয়া থাকি, উহা মহাশূন্য বটে। চাঁদ, সূর্য ও তারকারা সকলেই মহাশূন্যে অবস্থিত আছে, এমনকি এই পৃথিবীও।
মহাকাশের নীল রংটি সমুদ্রের জলে প্রতিফলিত হওয়ায় সমুদ্রের জল নীলবর্ণ বলিয়া ভ্রম হয়। সাগরজলের এই বর্ণটি আকাশে দেখিয়া একদল মানুষ মনে করিতেন, আকাশ জলের তৈয়ারী। তাহারা আরও মনে করিতেন –আকাশ প্রথমটি জলের, দ্বিতীয়টি লৌহের, তৃতীয় তারে, চতুর্থ স্বর্ণের ইত্যাদি। তাহারা জানিতেন না যে, সূর্যরশ্মির সপ্তবর্ণের একটি বর্ণ (নীল বর্ণ) বায়ুস্তরে আটকা পড়ায় ঐ নীল বর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে।
আদি (১; ২) –“পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপর অবস্থিতি করিতেছিলেন।” (এই বর্ণনাটি মনুসংহিতার ১; ৮-এর বর্ণনার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ)।
আলোচ্য সময় পর্যন্ত মাত্র দুইটি বস্তুই সৃষ্ট হইয়াছিল। একটি আকাশ, অপরটি পৃথিবী। অথচ এইখানে বলা হইতেছে যে, “পৃথিবী অন্ধকার জলধির উপরে ছিল”, এই জলধিটি বানাইল কে এবং কোন্ সময়ে, তাহা বুঝা যায় না।
পৃথিবীর সব অঞ্চলেই মাটিতে গর্ত বা কূপ খনন করিলে (বিভিন্ন গভীরতায়) জল পাওয়া যায়। ইহা দেখিয়াই বোধ হয় সেকালের লোকে মনে করিত, পৃথিবী জলের উপর অবস্থিত।
আদি (১; ৩-৫) –“পরে ঈশ্বর কহিলেন, ‘দীপ্তি হউক; তাহাতে দীপ্তি হইল। তখন ঈশ্বর দীপ্তি উত্তম দেখিলেন এবং ঈশ্বর অন্ধকার হইতে দীপ্তি পৃথক করিলেন। আর ঈশ্বর দীপ্তির নাম ‘দিবস’ ও অন্ধকারের নাম ‘রাত্রি’ রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে প্রথম দিবস হইল।”
এইখানে দেখা যায় যে, সূর্য সৃষ্টির আগে শুধু ঈশ্বরের মুখের কথায়ই সন্ধ্যা ও সকাল অর্থাৎ দিন ও রাত্রি হইল।
আদি (১; ৬-৮) –“পরে ঈশ্বর কহিলেন, জলের মধ্যে বিতান (শূন্য) হউক ও জলকে দুইভাগে পৃথক করুক। ঈশ্বর এইরূপে বিতান করিয়া বিতানের উদ্ধৃস্থিত জল হইতে বিতানের অধঃস্থিত জল পৃথক করিলেন। তাহাতে সেইরূপ হইল। পরে ঈশ্বর বিতানের নাম আকাশমণ্ডল রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে দ্বিতীয় দিবস হইল।”
এইখানে কি যে বলা হইল, সহজবুদ্ধি মানুষের পক্ষে তাহা বুঝা কঠিন।
আদি (১; ৯-১০) — “পরে ঈশ্বর কহিলেন, আকাশমণ্ডলের নীচস্থ সমস্ত জল একস্থানে সংগৃহীত হউক ও স্থল সপ্রকাশ হউক; তাহাতে সেইরূপ হইল। তখন স্থলের নাম ভূমি ও জলরাশির নাম সমুদ্র রাখিলেন।”
এইখানে বলা হইতেছে যে, আকাশমণ্ডলের নীচস্থ সমস্ত জল একস্থানে সংগৃহীত হউক। তাহাই যদি হয় তবে ভিন্ন ভিন্ন সমুদ্র, নদ-নদী ও হ্রদাদির সৃষ্টি হইল কি রকমে!
আদি (১; ১১-১৩) — “পরে ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি, তৃণ, বীজোৎপাদক ওষধি ও সবীজ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী ফলের বৃক্ষ ভূমির উপরে উৎপন্ন হউক; তাহাতে সেইরূপ হইল। ফলত ভূমি তৃণ, স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী বীজোৎপাদক ওষধি ও স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী সবীজ ফলের উৎপাদক বৃক্ষ উৎপন্ন করিল। আর ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম। আর সন্ধ্যা আর প্রাতঃকাল হইলে তৃতীয় দিন হইল।”
এইখানে দেখা যাইতেছে যে, সৃষ্টির তৃতীয় দিনে তৃণ ও গাছপালা জন্মিল। কিন্তু এই সময় পর্যন্ত সূর্য ও বাতাস সৃষ্টি হওয়ার কোনো বিবরণ নাই। অধুনা দেখা যাইতেছে যে, সূর্যালোক ও বাতাস (কার্বন ডাই-অক্সাইড) ভিন্ন কোনো উদ্ভিদ জন্মিতে বা বঁচিতে পারে না। সেই সময় উহা সম্ভব হইল কি রকমে!
আদি (১; ১৪–১৯) –“পরে ঈশ্বর কহিলেন, রাত্রি হইতে দিবসকে বিভিন্ন করণার্থে আকাশমণ্ডলের বিতানে জ্যোতির্গণ হউক। সে সমস্ত চিহ্নের জন্য, ঋতুর জন্য এবং দিবসের ও বৎসরের জন্য হউক এবং পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য দীপ বলিয়া আকাশমণ্ডলের বিতানে থাকুক; তাহাতে সেইরূপ হইল। ফলত ঈশ্বর দিনের উপর কর্তৃত্ব করিতে এক মহাজ্যোতি ও রাত্রির উপর কর্তৃত্ব করিতে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এক জ্যোতি, এই দুই বৃহৎ জ্যোতি এবং নক্ষত্রসমূহ নির্মাণ করিলেন। আর পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য এবং দিবস ও রাত্রির উপরে কর্তৃত্ব করণার্থে এবং দীপ্তি হইতে অন্ধকার বিভিন্ন করণার্থে ঈশ্বর ঐ জ্যোতিসমূহকে আকাশমণ্ডলের বিতানে স্থাপন করিলেন এবং ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম। আর সন্ধ্যা আর প্রাতঃকাল হইলে চতুর্থ দিবস হইল।”
প্রিয় পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, আদিপুস্তকের ১; ৩–৫-এ লিখিত আছে, “পরে ঈশ্বর কহিলেন, ‘দীপ্তি হউক; তাহাতে দীপ্তি হইল। … আর ঈশ্বর দীপ্তির নাম দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন।” এইখানে আবার দেখা যায় যে, চাঁদ, সূর্য ও নক্ষত্রের দ্বারা দীপ্তি সৃষ্টি করিলেন, দীপ্তি হইতে অন্ধকার ভিন্ন করিয়া পুনঃ দিন ও রাত্রি সৃষ্টি করিলেন।
প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়, এই তিনটি ‘দিন’-এর সৃষ্টি হইয়াছিল ঈশ্বরের মহিমা বা কুদরতি আলোকে এবং চতুর্থ দিবসটির সৃষ্টি হইল সৌরালোকে। সূর্যের আলো ও কুদরতি আলো– ইহাতে পার্থক্য কি এবং কুদরতি আলোয় দিন হওয়ার নিয়ম বাতিল করিয়া সৌরালোকে দিন হওয়ার নিয়ম কেন কায়েম করা হইল, তাহা বুঝা মুশকিল। কুদরতি আলোকে তাপ ছিল না, তাই উহা জীবজগতের অনুকূলও ছিল না; বোধ হয় এই কারণেই উহা বাতিল করা হইয়াছে।
আজকাল শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রই জানেন যে, নক্ষত্রগণ কেহই ক্ষুদ্র আলোর বিন্দু নহে। উহারা প্রত্যেকেই এক একটি সূর্য। কোনো কোনো নক্ষত্র সূর্য অপেক্ষা ছোট, কিন্তু অধিকাংশই সূর্য অপেক্ষা বড়। কোনো কোনো নক্ষত্র সূর্য অপেক্ষা হাজার, লক্ষ বা কোটি কোটি গুণ বড়। সূর্যের ব্যাস মাত্র (প্রায়) ৮ লক্ষ ৬৬ হাজার মাইল। কিন্তু মহাকাশে বেটেল জিউস নামক নক্ষত্রটির ব্যাস প্রায় ২১ কোটি মাইল। কয়েক লক্ষ সূর্য উহার পেটের মধ্যে লুকাইয়া থাকিতে পারে। Omicron Ceti নামক নক্ষত্রটি আয়তনে প্রায় তিন কোটি সূর্যের সমান এবং অ্যান্টারেস নামক নক্ষত্রটির আয়তন প্রায় ১০ কোটি সূর্যের সমান। পক্ষান্তরে চন্দ্র এতোধিক ছোট যে, নক্ষত্রদের সহিত উহার। তুলনাই হয় না। যেহেতু ৫০টি চন্দ্র একত্রিত না করিলে পৃথিবীকে পড়া যায় না এবং পৃথিবী হইতে সূর্য প্রায় ১৩ লক্ষ গুণ বড়। অর্থাৎ চন্দ্র সূর্যের সাড়ে ছয় কোটি ভাগের এক ভাগ মাত্র। অথচ কোটি কোটি অতিকায় মহাজ্যোতিষ্কদের সাধারণ নক্ষত্র বলিয়া, চন্দ্র ও সূর্যকে বলা হইয়াছে “এই দুই বৃহৎ জ্যোতি”। অর্থাৎ মানুষ তাহার সাধারণ দৃষ্টিতে যেরূপ দেখিয়া থাকে, উহা তাহাই।
সৃষ্টিকর্তা চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রদের প্রকৃত অবয়ব সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অবহিত ছিলেন বা আছেন; অবগত ছিল না শুধু মানুষ, দূরবীন আবিষ্কারের পূর্বে। উহাদের সম্পর্কে এখন মানুষের ধারণার পরিবর্তন হইয়াছে এবং সঠিক জ্ঞান জন্মিয়াছে। সে যাহা হউক, উপরোক্ত বর্ণনাটি মানবীয় জ্ঞানেরই পরিচায়ক, ঐশ্বরিক জ্ঞানের নহে।
আদি (১; ২০-২৪) — “পরে ঈশ্বর কহিলেন, জল নানা জাতীয় জঙ্গম প্রাণীবর্গে প্রাণীময় হউক এবং ভূমির উর্ধে আকাশমণ্ডলের বিতানে পক্ষীগণ উড়ুক। তখন ঈশ্বর বৃহৎ তিমিগণের ও যে নানা জাতীয় জগম প্রাণীবর্গে জল প্রাণীময় আছে, সে সকলের এবং নানা জাতীয় পক্ষীর সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম। আর ঈশ্বর সে সকলকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত হও ও বহুবংশ হও, সমুদ্রের জল পরিপূর্ণ কর এবং পৃথিবীতে পক্ষীগণের বাহুল্য হউক। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে পঞ্চম দিবস হইল।”
আদি (১; ২৫-২৭) –“পরে ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি নানা জাতীয় প্রাণীবর্গ অর্থাৎ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গ্রাম্য পশু, সরীসৃপ ও বন্য পশু উৎপাদন করুক; তাহাতে সেইরূপ হইল। ফলত ঈশ্বর স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী বন্য পশু ও স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গ্রাম্য পশু ও স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী যাবতীয় ভূচর সরীসৃপ নির্মাণ করিলেন। আর ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম। পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি। আর তাহারা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্তৃত্ব করুক। পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন, ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন। … আর সন্ধ্যা ও। প্রাতঃকাল হইলে ষষ্ঠ দিবস হইল।”
পূর্বোক্ত বিবরণগুলিতে জানা যায় যে, ঈশ্বর পঞ্চম দিনে সৃষ্টি করিলেন জগতের যাবতীয় জলচর ও খেচর প্রাণী এবং ষষ্ঠ দিনের সম্ভবত সকাল বেলা সৃষ্টি করিলেন যাবতীয় ভূচর প্রাণী। ঐ সমস্ত জীব সৃষ্টি করিতে ঈশ্বর কোনোই উপাদান ব্যবহার করেন নাই, ব্যবহার করিয়াছেন শুধু কথা। বিশেষত কোনো প্রাণী সৃষ্টি করিতেই তাহার একাধিক দিন সময় লাগে নাই। আর অধুনা একটি হস্তী সৃষ্টি করিতে দুই বৎসর, একটি মানুষ বা গরু সৃষ্টি করিতে নয় মাস (চলিত কথায় দশ মাস), একটি ছাগল ছয় মাস, কুকুর তিন মাস এবং একটি মশা সৃষ্টি করিতেও ঈশ্বরের প্রায় দুই সপ্তাহ সময় লাগে।
ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করিলেন সম্ভবত ষষ্ঠ দিনের বিকাল বেলা, নিজের আকৃতিতে। এই অনুচ্ছেদে তিনবারই উল্লিখিত হইয়াছে যে, ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করিলেন নিজের প্রতিমূর্তিতে। ইহাতে বুঝা যায় যে, ঈশ্বর মানুষের আকৃতিবিশিষ্ট জীব। কেননা আদিপুস্তকের ১; ২-এ লিখিত আছে যে, ঈশ্বরের আত্ম জলের উপর অবস্থিতি করিতেছিলেন। যে ঈশ্বর মানুষের। আকৃতিবিশিষ্ট এবং আত্মা বা জীবন ধারণ করেন, তিনি হ’ন জীবশ্রেণীভুক্ত এবং তিনি নিরাকার নহেন, নরাকার।
আদি (২; ১/১) –“এইরূপে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং বস্তুব্যুহ সমাপ্ত হইল। পরে ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপনার কৃতকার্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন। সেই সপ্তম দিনে আপনার কৃত সমস্ত কার্য হইতে বিশ্রাম করিলেন।”
ছয় দিন কাজ করিয়া ঈশ্বর সপ্তম দিনে বিশ্রাম করিলেন। অসীম শক্তিসম্পন্ন নিরাকার ঈশ্বরের পক্ষে না হইলেও নরাকার ঈশ্বরের পক্ষে পরিশ্রমে ক্লান্ত হওয়া স্বাভাবিক, কাজেই বিশ্রাম আবশ্যক। হয়তো কেহ বলিতে পারেন যে, ঐ বিশ্রাম তাঁহার কায়িক বা মানসিক শ্রান্তিজনিত নহে, উহা তাঁহার কার্য হইতে বিরত থাকা।
আলোচ্য ছয় দিনে ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়াছিলেন একটি চন্দ্র, একটি সূর্য, একটি পৃথিবী ও হাজার ছয়েক নক্ষত্র (ছয় হাজারের বেশি নক্ষত্র খালি চোখে দেখা যায় না) এবং যাবতীয় জীবের এক এক জোড়া করিয়া জীব মাত্র। আর বর্তমানে মহাকাশে দেখা যাইতেছে দশটি পৃথিবী (গ্রহ), গোটা ত্রিশেক চন্দ্র (উপগ্রহ) ও হাজারো কোটি সূর্য (নক্ষত্র)। হয়তো ঐ সকল সূর্যেরও গ্রহ-উপগ্রহ থাকিতে পারে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, ঈশ্বর এই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন আদিসৃষ্টির পরে এবং এখনও মহাকাশে নূতন নূতন নক্ষত্র ও নীহারিকা সৃষ্টি করিতেছেন। আর জীবসৃষ্টি ঈশ্বর ঐ ছয়দিনে যাহা করিয়াছেন, বর্তমানে প্রতি মিনিটে করেন তাহার চেয়ে বেশি। মশা, মাছি বা পিপীলিার কথা তুলিলাম না। আলোচ্য ছয়দিনে ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন মাত্র দুইটি, আর বর্তমানে প্রতি মিনিটে সৃষ্টি করিতেছেন প্রায় ৪২টি। তথাপি সেই দিন হইতে এখন পর্যন্ত ৫,৯৭৪ বৎসরে তিনি দ্বিতীয়বার বিশ্রামের নামও লইলেন না (বাইবেলের মতে, আদম বা জগত সৃষ্ট হইয়াছিল খ্রী. পূ. ৪০০৪ সালে[২] এবং বর্তমানে ১৯৭০ সাল)।
আজ প্রত্যেক ব্যক্তি অবগত আছেন যে, লোকসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধির ফলে ক. পৃথিবীময় খাদ্যসংকট দেখা দিয়াছে এবং উহার প্রতিকারের জন্য রাষ্ট্রনেতাগণ জন্মনিয়ন্ত্রণ বিধি প্রবর্তনে বাধ্য হইতেছেন। ইহাতে মানব জাতির ভবিষ্যত কল্যাণের পথ পরিষ্কার হইতেছে বটে, কিন্তু গোড়া ধার্মিকগণ ইহাতে ‘মহাপাপ মহাপাপ’ বলিয়া হৈ চৈ করিতেছেন। এমতাবস্থায় ঈশ্বর যদি প্রতি সপ্তাহের বিশ্রামবারে অন্তত মানুষ সৃষ্টির কাজে বিরত থাকিয়া বিশ্রাম লইতেন, তবে বিশ্বমানবের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইত।
ঈশ্বর বিশ্রাম লইয়াছিলেন মাত্র এক রোজ শনিবার আর বনিআদমকে বিশ্রাম লইতে বলিয়াছেন চিরকালের শনিবার। ঐদিন দুনিয়ার যাবতীয় কাজকর্ম হইতে বিরত থাকার হুকুম দিয়াছেন ঈশ্বর এবং উহা অমান্যকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। ইহুদি জাতি উহা পুরাপুরিই পালন করিতেছেন এবং অন্যান্য সেমিটিক জাতিও কিছুটা পালন করেন, হয়তো একদিন আগে বা পরে। কিন্তু আলোচ্য বিশ্রামবার হাল জামানায় আন্তর্জাতিকভাবে দাঁড়াইয়াছে রবিবারে।
আদি (২; ৭) –“আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে নির্মাণ করিলেন এবং তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন, তাহাতে মনুষ্য সজীব প্রাণী হইল।”
বাইবেলের (আদিপুস্তকে) সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনায় বায়ু ও অগ্নি সৃষ্টির কোনো উল্লেখ দেখা যায় না। ঈশ্বর ফুঁ দিয়া আদমের দেহে যে প্রাণ-বায়ু প্রবেশ করাইলেন, উহা বায়ুর ব্যবহার মাত্র, সৃষ্টি নহে। উহাতে মনে হয় যে, হয়তো ঈশ্বর বায়ু ও অগ্নি সৃষ্টি করেন নাই, নচেৎ বাইবেল লেখকের ভুল।
আদি (২; ৮) –“আর সদাপ্রভু ঈশ্বর পূর্বদিকে এদনে, এক উদ্যান প্রস্তুত করিলেন এবং সেই স্থানে আপনার নির্মিত ঐ মনুষ্যকে রাখিলেন।”
অত্র বিবরণে দেখা যায় যে, আদমের বাসস্থান ‘এদন’ পূর্বদিকে অবস্থিত? কিন্তু কোন্ স্থান হইতে পূর্ব, তাহার উল্লেখ নাই।
আদি (২; ২১-২২)– “পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ঘোরনিদ্রায় মগ্ন করিলেন, তিনি নিদ্রিত হইলেন, আর তিনি তাঁহার একখানা পঞ্জর লইয়া মাংস দ্বারা সেই স্থান পুরাইলেন। সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম হইতে গৃহীত সেই পঞ্জরে এক স্ত্রী নির্মাণ করিলেন ও তাহাকে আদমের নিকটে আনিলেন।”
আদমকে ঘোরনিদ্রায় অভিভূত করিয়া তাহার বক্ষের অস্থি গ্রহণ করা ডাক্তারদের ক্লোরোফরম দ্বারা অপারেশন করারই অনুরূপ। তবে ক্লোরোফরম ব্যতীত সম্মোহন (Hypnotism) শক্তির দ্বারাও মানুষকে গভীর নিদ্রায় অভিভূত করা যায় এবং তদবস্থায় অপারেশন করাও চলে। কিন্তু এইখানে প্রশ্ন থাকিল এই যে, আদমের বক্ষের অস্থি গ্রহণ করা হইল কোনো অস্ত্রের দ্বারা কাটিয়া, ছিঁড়িয়া?
আদমের শরীর গঠন করা হইল ধূলি বা মাটির দ্বারা। কিন্তু অন্যান্য জীবাদিসৃষ্টি কি দিয়া হইল, তাহার কোনো উল্লেখ নাই; বোধ হয় অন্য কিছু। অথচ মানুষ ও পশু-পাখির রক্ত, মাংস, অস্থি-মজ্জা ইত্যাদিতে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না।
আদম ভিন্ন অন্য কোনো জীব সৃষ্টি করিতেই ঈশ্বরের কোনো উপাদানের দরকার হয় নাই। আদিনারী সৃষ্টির কাজে উপাদান লাগিল কেন এবং উপাদান লাগিলেও মাটি-পাথরাদি নানাবিধ। মশলা থাকিতে আদমের অঙ্গহানি করার আবশ্যক ছিল কি?
বলা যাইতে পারে যে, পুরুষের অঙ্গ হইতে নারীর সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াই নারী ও পুরুষ এর অগাভি সম্পর্ক। কিন্তু দেখা যায় যে, পশু-পাখিদেরও স্ত্রী-পুরুষে প্রেমের বন্ধন যথেষ্ট এবং মানুষের মধ্যেও স্ত্রী ত্যাগ করা (তালাক) অপ্রতুল নহে।
.
# বৌদ্ধ ধর্ম
বৌদ্ধরা বলেন যে, এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা কেহ নাই; জগত অনন্তকাল বিদ্যমান আছে এবং থাকিবে। চিরকালই বিশ্বের আকৃতি একরূপ আছে এবং থাকিবে। কর্মানুসারে প্রাণীসমূহ সংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে মাত্র।
.
# ইসলাম ধর্ম
মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ পবিত্র কোরানের মতে, নির্দিষ্ট কালে আল্লাহ কর্তৃক পৃথিবী সৃষ্ট হইয়াছে। এবং নির্দিষ্ট সময়ে উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।
সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে পবিত্র কোরানের বহুস্থানেই বিক্ষিপ্তভাবে অধিক বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা
সুরা সেজদা (১; ৪) –“তিনি আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আছে, তাহা ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন।”
সুরা সেজদা (৭ আয়াত) –“তিনিই মৃত্তিকা হইতে মানবসৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন।”
সুরা সাফফাত (৬)— “নিশ্চয় আমি পার্থিব আকাশকে নক্ষত্রপুঞ্জের শোভায় শোভিত করিয়াছি।”
সুরা হামিম (৯/১০/১২) — “তোমরা কি তাহার প্রতি অবিশ্বাস করিতেছ –যিনি দুই দিনে এই পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন … এবং তিনি তন্মধ্যে উহা হইতে সমুচ্চ পর্বতমালা সৃষ্টি করিয়াছেন এবং চারি দিবসে তন্মধ্যে উহার উৎপাদিকা শক্তি নির্ধারিত করিয়াছেন। … অনন্তর তিনি দুই দিবসের মধ্যে সপ্ত আকাশ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।”
সুরা ক্বাফ (৩৮) –“নিশ্চয়ই আমি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এতদুভয়ের অন্তর্গত বিষয়সমূহ ছয় দিবসে সৃষ্টি করিয়াছি।” ইত্যাদি।
মুসলমানদিগের ধর্মগ্রন্থমতে সৃষ্ট প্রাণীর চারিটি স্তর। যথা –ফেরেশতা, জ্বীন, মনুষ্য ও শয়তান।
ফেরেশতা বা স্বর্গীয় দূত –তাহারা অগ্নি (নূর) হইতে উৎপন্ন; তাহারা নির্মল এবং বিভিন্ন আকৃতি ধারণে সমর্থ। তাহাদের পানাহারের প্রয়োজন হয় না এবং তাহাদের (মানুষের মতো) জন্ম-মৃত্যু নাই, তাহাদের সন্তান-সন্ততি জন্মগ্রহণ করে না। জেব্রাইল, মেকাইল, এস্রাফিল ও আজরাইল স্বর্গীয় দূতগণের মধ্যে প্রধান স্থানীয়।
জ্বীন –উহাদের জন্ম-মৃত্যু এবং নারী-পুরুষ ভেদ ও সন্তান-সন্ততিও আছে। উহাদের পাপ পুণ্যের ফলাফলস্বরূপ স্বর্গ বা নরকবাসও নির্ধারিত আছে। উহারা নাকি ধূমশূন্য অগ্নির দ্বারা তৈয়ারী। এবং মরুদেশের বাসিন্দা। উহারা দৈত্য-দানবের ন্যায় অনিষ্টকারী।
মনুষ্য –ইহাদের আদিপুরুষ আদম। আদমের সৃষ্টি সম্বন্ধে কথিত হয় যে, আদমকে সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আল্লাহ ফেরেশতাদের মতামত জানিতে চাহিলে, “ফেরেশতাদের ন্যায় আদমের বংশধরগণ আল্লাহর অনুগত থাকিবে না” –এই বলিয়া তাহারা আদম সৃষ্টিতে অমত জানায়। তথাপি আল্লাহ আদম সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কিছু মাটি লইবার জন্য এস্রাফিলাদি ফেরেশতাগণকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। তাহারা আদম সৃষ্টির জন্য মাটি চাহিলে, মাটি এই বলিয়া দোহাই দেয় যে, আদম জাতি আল্লাহর অবাধ্য হইবে এবং তাহাদের দ্বারা দোজখ পূর্ণ করা হইবে। সুতরাং মাটি আদমের দেহের উপকরণ হইয়া দোজখের শাস্তি ভোগ করিতে রাজি নহে। ইহা শুনিয়া একে একে তিন ফেরেশতা খালি হাতে ফিরিয়া যায় এবং শেষে আজরাইল ফেরেশতা পৃথিবীতে আসিয়া মাটির দোহাই অগ্রাহ্য করিয়া জোরপূর্বক কিছু মাটি লইয়া যায়। আজরাইল ফেরেশতার প্রভুর আদেশ পালন, কর্তব্যনিষ্ঠা, অনমনীয় মনোবল ইত্যাদি গুণের জন্য আল্লাহ তাহাকে মানুষের জীবন হরণ (জান কবজ) করিবার কাজে নিয়োগ করেন। অতঃপর বিশ্বসৃষ্টির ষষ্ঠ দিনের বিকাল বেলা বৈকালিক উপাসনার পর পবিত্র মক্কার মাটি দ্বারা আল্লাহ আদমের শরীর তৈয়ার ও তাহাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন।
অতঃপর আদমের দেহস্থ খানিকটা অংশ লইয়া হাওয়া নাম্নী একটি নারী তৈয়ার করিয়া উভয়কে থাকিবার জন্য আল্লাহ বেহেশতে স্থান দান করেন। বেহেশতে থাকাকালীন আল্লাহর হুকুম অমান্য করিয়া গন্ধম নামক ফল ভক্ষণের অপরাধে আদম সপরিবারে নির্বাসিত হন পৃথিবীতে। সন্ধীপ নামক স্থানে আদম পতিত হন ও বিবি হাওয়া নিপতিত হন জেদ্দায় এবং বহু বৎসর পরে তাঁহাদের পুনর্মিলন হয় আরাফাত-এ। সেখানে থাকিয়া তাহাদের সন্তান-সন্ততি জন্মিয়াছে ১২০টি এবং তাহাদেরই বংশাবলীতে পৃথিবী মানুষে ভরপুর। আদমের বংশজাত বলিয়া মানুষকে বলা হয় ‘আদমী’ (হিন্দুগণ বলিয়া থাকেন যে, মনুর বংশজাত বলিয়া উহারা মানব’)।
উপরোক্ত ঘটনাবলীর স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ বলা হয় যে, বিবি হাওয়া গন্ধম ফল ছিড়িলে, উহাতে সেই গাছটি ব্যথা পাইয়াছিল ও ছিন্ন বোটা দিয়া কষ ঝরিতেছিল। তাই গন্ধম বৃক্ষ বিবি হাওয়াকে এই বলিয়া অভিশপ্ত করে যে, তাহার দেহ হইতেও প্রতি মাসে একবার কিছু একটা ক্ষরণ হইবে এবং সে সন্তান প্রসবান্তে ব্যথায় কষ্ট পাইবে। বর্তমান মানবীদের ‘মাসিক ঋতু এবং প্রসবান্তে ‘হ্যাতাল ব্যথা’ –উভয়ই নাকি গন্ধম বৃক্ষের অভিশাপের ফল। আরও বলা হয় যে, আদমের বাম পঞ্জরাস্থির দ্বারা বিবি হাওয়াকে নির্মাণ করা হইয়াছিল, সেই জন্য নাকি পুরুষ মানুষের বাম পঞ্জরে একখানা অস্থি কম।
শয়তান— শয়তান পূর্বে ছিল মকরম নামক বেহেসী একজন প্রথম শ্রেণীর ফেরেশতা। মকরম সেখানে খোদাতালার আদেশমতো আদমকে সেজদা না করায় ‘শয়তান’ আখ্যা পাইয়া চিরকাল আদম-বংশকে অসৎকাজে প্ররোচনা দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করিয়া পৃথিবীতে আসে। এবং সে অদ্যাবধি মানুষকে অসৎকাজে প্ররোচনা (দাগা) দিয়া বেড়াইতেছে।
কেহ কেহ বলেন যে, শয়তান উভলিঙ্গ জীব। উহার এক উরুতে পুংলিগ এবং অপর উরুতে স্ত্রীলিগ। উরুদ্বয়ের সম্মিলনেই শয়তানের গর্ভসঞ্চার হয় এবং প্রতি গর্ভে সন্তান জন্মে দশটি করিয়া। উহাদের নাম হয় যথাক্রমে –জলিতন, ওয়াসিন, নফস, আওয়াম, আফাফ, মকার, মসুদ, দাহেম, ওলহান ও বার। ইহারা ক্ষেত্রবিশেষে থাকিয়া প্রত্যেকে বিশেষ বিশেষ দাগাকার্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। বিশেষত উহাদের মানুষের মতো মরণ নাই। যেদিন মানব জাতি লয় পাইবে (কেয়ামতের দিন), সেই দিন শয়তানদের মৃত্যু ঘটিবে।
পবিত্র কোরানের প্রসিদ্ধ অনুবাদক ডক্টর সেল অনুসন্ধান করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, “স্বর্গদূত সংক্রান্ত অভিব্যক্তিতে মোহাম্মদ (সা.) ইহুদিদিগের মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এদিকে ইহুদিগণ আবার পারসিকদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন।” জ্বীন সম্বন্ধে তিনি বলেন, “ইহুদিদিগের মধ্যে শেদিম (Shedim) নামক এক শ্রেণীর দৈত্যের পরিচয় পাওয়া যায়; জ্বীনগণ উহাদেরই রূপান্তর।”
০৩. দার্শনিক মতে সৃষ্টিতত্ত্ব
দার্শনিক মতে সৃষ্টিতত্ত্ব
সভ্যতার উষাকাল হইতেই মানুষ ভাবিত, এই অসংখ্য বৃক্ষ-লতা ও জীবসমাকুল পৃথিবী সৃষ্টি করিল কে? চন্দ্র-সূর্য, আকাশ ও নক্ষত্র সৃষ্টি করিল কে? নিত্য নূতন সৃষ্টি ও পুরাতনকে রক্ষা করে কে?
প্রশ্ন যেমন হইল, তেমন সমাধানও হইল। মানুষের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী এক জীব সৃষ্টি করিয়াছেন –মানুষ, পশু, পাখি, মাটি-পাথর, আকাশ, বাতাস সবই। উহা রক্ষা ও প্রতিপালন তিনিই করিয়া থাকেন। কেহ বলিল, সৃষ্টিকর্তা এক; আবার কেহ বলিল, অনেক। যাক সেই কথা। তাহার বা তাহাদের নাম রাখা হইল ‘ঈশ্বর’ বা ‘দেবতা।
গেল বেশ কিছুদিন। মানুষের সন্ধানী মন আবার জানিতে চাহিল, ওইসব সৃষ্ট হইল কি দিয়া? আকাশ, বাতাস, মাটি, পানি, রকমারি জীবসমাকুল পৃথিবীর উপাদান কি?
জগত সৃষ্টি কে করিয়াছেন, এই প্রশ্নের সমাধান যত সহজে হইয়া গেল, কি দিয়া সৃষ্ট হইয়াছে, এই প্রশ্নের সমাধান. তত সহজে হইল না। ‘কে’ ও ‘কি দিয়া’, এই উভয় প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টা করিয়াছে ‘দর্শন’। কিন্তু সকল দার্শনিক একমত হইতে পারেন নাই। ইহাতে বহু দার্শনিক বহু মতবাদ প্রচার করিয়াছেন এবং বহু দার্শনিক সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছে। কেননা কোনো দার্শনিকই ধর্মজগতের আবহাওয়ার আওতার বাহিরের মানুষ ছিলেন না। তথাপি দার্শনিকগণ সাধারণত দুই শ্রেণীর –ধর্মীয় আওতাভুক্ত ও মুক্ত। এইখানে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশের কয়েকজন দার্শনিকের মতবাদের আলোচনা করিতেছি।
থেলিস (জন্ম খ্রী. পূ. ৬৪০) –ইনি গ্রীস দেশের আদি দার্শনিক। ইনি বলিতেন, “জলই সংসারের সার-সর্বস্ব। জল হইতেই এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি হইয়াছে; জলেই সংসার লয়প্রাপ্ত হইবে।”
আনাক্সিমান্দর (খ্রী. পূ. ৬১০–৫৪৬) –ইনি দার্শনিক থেলিসের শিষ্য। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে ইহার মত –“বিশ্ব অনন্তকাল বিদ্যমান। তাহার অংশবিশেষের পরিবর্তন সাধিত হইতেছে মাত্র। অনন্তকাল হইতে সকল বস্তুর উদ্ভব। অনন্তেই সকল বস্তু বিলীন হইবে।” তাঁহার মতে, জগতের মূল পদার্থ নিত্য, অসীম এবং তাহা নির্দেশ করা যায় না।
পিথাগোরাস (জন্ম খ্রী. পূ. ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ)– ইতালির স্যামজ দ্বীপের অধিবাসী এই দার্শনিক সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বলিতেন, “বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে এক অগ্নিপিণ্ড বিদ্যমান আছে। দশটি স্বর্গীয় গ্রহ বা উপগ্রহ তাহার চতুর্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তদ্বারা শীত, উত্তাপ প্রভৃতির সঞ্চারে সৃষ্টিকার্য সমাহিত হইতেছে। সামঞ্জস্যই জগতের অস্তিত্ব। সেই কেন্দ্রীভূত অগ্নিপিণ্ডই তাপ, আলোক বা প্রাণ স্থানীয়। জীবাত্মা মাত্রই সেই অগ্নিপিণ্ডের বা তেজের অংশবিশেষ। সর্বপ্রাণাধার সেই তেজ বা অগ্নিপিণ্ডই ঈশ্বর। ঈশ্বর প্রথমে অব্যবস্থাপিত জড় পদার্থ সহ বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার শক্তিপ্রভাবে তৎসমুদয় বিচ্ছিন্ন হয়। বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তিনি পৃথকভাবে অবস্থিত আছেন।”
আত্মার দেহান্তর গ্রহণ পিথাগোরাস স্বীকার করিতেন। ঈশ্বরকে মনঃস্বরূপ বলিয়া তিনি প্রচার করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিতেন, “সংসারে সকলের মধ্যেই তিনি (ঈশ্বর) বিদ্যমান। প্রত্যেক মানুষের আত্মাই তাহার অংশ।” পরবর্তী অনেক দার্শনিক পিথাগোরাসের মত মান্য করিয়াছিলেন এবং কোনো কোনো ধর্মবেত্তাও।
পিথাগোরাসের বিশ্বরূপ ও সৃষ্টিতত্ত্ব আধুনিক সৌরজগত ও সৌরবিজ্ঞানের সহিত বহুলাংশে সাদৃশ্যপূর্ণ।
জেনোফেনস (খ্রী. পূ. ৫৬০–৫৪০) –এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত কলফো নগরে দার্শনিক জেনোফেস্ জন্মগ্রহণ করেন। তাহার মতে, “এই বিশ্ব যেভাবে অবস্থিত দেখিতে পাইতেছি, সেইভাবেই চিরদিন বিদ্যমান আছে এবং থাকিবে।” জেনো চারি ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। তাহার মতে, “উত্তাপ ও আর্দ্রতা, শৈত্য ও শুষ্কতা –এই চারি ভূতে সংসার উৎপন্ন। মনুষ্য মৃত্তিকা হইতে নির্মিত। চারি ভূতের সংমিশ্রণে তাহার প্রাণশক্তি সঞ্চারিত।” জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি বিষয়ে বৌদ্ধরা জেনোর মতানুসারী।
হিরাক্লিটাস (জন্ম খ্রী. পূ. ৫০৩) –ইনি এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত ইফেসাস নগরে জন্মগ্রহণ করেন। হিরাক্লিটাসের দার্শনিক গ্রন্থে প্রকাশ, “তেজ (আগুন) হইতেই পৃথিবীর সৃষ্টি; আবার তেজেই বিশ্বের লয়। তেজ বা অগ্নি সূক্ষ, অনন্ত, অপরিবর্তনীয় এবং চির গতিবিশিষ্ট। অগ্নিরই স্থূলতর অংশ বায়ু; বায়ু হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি। আত্মা বা প্রাণ জ্বলনশীল অথবা বায়বীয় পদার্থ।”
এম্পিডোকলস (খ্রী. পূ. ৪৫০) –ইনি সিসিলি দ্বীপের এগ্রিজেন্টাস নগরের অধিবাসী। ঘঁহার মতে, “বায়ু, জল, অগ্নি, পৃথিবী (মাটি) — এই চারি পদার্থের সংযোগ-বিয়োগেই এই পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমে ঐ চারি মূল পদার্থ একরূপ মিশ্রভাবে অবস্থিত থাকে। উহারা পরস্পর ভালোবাসা (আকর্ষণ) সূত্রে আবদ্ধ ছিল। যখন পরস্পরের মধ্যে ঘৃণার (বিকর্ষণের) সঞ্চার হইল, তখনই উহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। সেই বিচ্ছেদের ভিন্ন ভিন্ন স্তরে পৃথিব্যাদি বিভিন্ন সামগ্রীর সৃষ্টিক্রিয়া সাধিত হইয়াছে।” বিশ্বসৃষ্টির মৌলিক উপাদান চারিটি, ইহা মুসলিম জগতেও স্বীকৃত। যথা –আব, আতস, খাক, বাত।
আনাক্সীগোরাস (জন্ম খ্রী. পূ. ৫০০) –আইওনিয়ার অন্তর্গত ক্রেজোমিনি নগরে হঁহার জন্ম হয়। সৃষ্টি সম্বন্ধে তাঁহার মত –“আদিতে অনন্তকাল হইতে সকল পদার্থই পরমাণুরূপে বিদ্যমান ছিল। সেই অসংখ্য পরমাণুপুঞ্জ এক অনন্ত শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া নানা আকার ধারণ করিতেছে। সেই অনন্ত শক্তির নাম ‘নৌস’। নৌস অবিমিশ্র ও সূক্ষ্ম, অনন্ত শক্তিসম্পন্ন এবং সর্বজ্ঞানাধার। আপনা-আপনি অন্ধ শক্তির দ্বারা পৃথিবীর কোনো বস্তু সৃষ্ট হয় নাই; নৌসই সকল সামগ্রীর সর্ববিধ আকৃতির সংগঠক। আকাশ স্থূল-পদার্থ-নির্মিত –খিলানের ন্যায় অবস্থিত। নক্ষত্রসমূহ এক একটি প্রস্তরপিণ্ড; কোনোরূপ পার্থিব আক্ষেপবশত ঊর্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছে। আকাশে গিয়া ইথারের অগ্নিসংযোগে তাহারা প্রতিনিয়ত জ্বলিতেছে।” সূর্যকে তিনি প্রকাণ্ড জ্বলন্ত প্রস্তরখণ্ড বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তিনি বলিতেন, “সে প্রস্তরখণ্ড গ্রীসের পেলোপোনিসাস নগর অপেক্ষাও বৃহত্তর।” তাহার মতে, “মনই সকল বস্তুর জনয়িতা; প্রথমে সকলই বিশৃঙ্খল ছিল, মন সকলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। মন অনন্ত শক্তিসম্পন্ন। মনই নৌস।”
ডেমক্রিটাস (খ্রী. পূ. ৪৬০)– গ্রেস প্রদেশের অব্দেরা নগরে ডেমক্রিটাস জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষা ও নানাদেশ পর্যটনান্তে দেশে ফিরিয়া একমনে দার্শনিক চিন্তায় কালাতিপাত করিতে পারিবেন বলিয়া তিনি আপনার চক্ষুদ্বয় উৎপাটন করিয়াছিলেন এবং অন্ধ হইয়া একমনে দার্শনিক চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। সৃষ্টি সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন, “পরমাণু এবং গতি, এতদুভয়ের উপর সৃষ্টি নির্ভর করিতেছে। কোনো উচ্চ শক্তি ইচ্ছা করিয়া যে পরমাণুসমূহকে একত্র করিতেছে, তাহা নহে; আপনা-আপনিই নৈসর্গিক নিয়মে গতি দ্বারা চালিত হইয়া পরমাণুসমূহ সম্মিলিত ও বিচ্ছিন্ন হইতেছে; আর তাহাতেই সৃষ্টিকার্য সাধিত হইতেছে।” অনেকের বিশ্বাস –ডেমক্রিটাস পাশ্চাত্য দেশে নিরীশ্বরবাদের প্রবর্তন করিয়া যান। ইনি পরমাণুবাদ তত্ত্বের আবিষ্কর্তা বলিয়া প্রসিদ্ধ। আবার কেহ কেহ বলেন যে, পরমাণুবাদ তত্ত্বের আবিষ্কর্তা লিউঁকিগ্লাস।
লিউকিপ্পাস (খ্রী. পূ. ৪৩০) –সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে লিউঁকিপ্পাসের মত এইরূপ — “বিশ্ব অনন্ত, ইহার কোনোও অংশ শূন্যতাময়, কোনোও অংশ পরমাণুপূর্ণ। পরমাণুসমূহ শূন্যস্থানে বিক্ষিপ্ত হইলে পরস্পর প্রতিহত হয় এবং তাহাদের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ চলিতে থাকে। তাহাতে শূন্যসাগরে বিষম আক্ষেপ উপস্থিত হয়। ফলে, এক এক জাতীয় পরমাণু পরস্পর মিলিত হয় এবং তাহাতে তাহাদের এক এক প্রকার আকৃতি গঠিত হইয়া যায়। আপনা-আপনি নিয়তিবশে এই বিক্ষেপ ও মিলন-ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে। ইহার সহিত কোনোও দৈবশক্তির সম্বন্ধ নাই।”
সক্রেটিস ও প্লেটো (খ্রী. পূ. ৪৬৯ ও ৪২৯) –সক্রেটিস ও প্লেটো, উভয়েই এথেন্স নগরের অধিবাসী ছিলেন। গ্রীসদেশীয় দার্শনিকগণের মধ্যে সক্রেটিস প্রখ্যাতনামা। তিনি ‘জ্ঞান’কেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাহার মতে, “ন্যায়পরতাই মানুষের ধর্ম।” সুতরাং ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্বে বা অস্তিত্বে তিনি সন্দিহান ছিলেন। তিনি দেশমান্য দেবতাগণের পূজা করিতেন না। তাহার মতের অনুসরণ করিয়া যুবকগণ বিপথগামী হইতেছে, এই অজুহাতে সক্রেটিস রাজদ্বারে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। ত্রিশ দিবস কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া তিনি বিষপানে প্রাণত্যাগ করেন। দেববিরোধিতার অপরাধে এরূপ অমানুষিক হত্যাকাণ্ড পাশ্চাত্য দেশে ইহা নূতন নহে। দার্শনিক আনাক্সাগোরাস দেব-দেবীর প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেন বলিয়া তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয় এবং তাহার শিষ্য পেরিক্লেসের বাগ্মিতায় বিচারপতি মুগ্ধ হইয়া আনাক্সাগোরাসের প্রাণদণ্ড রহিত করিয়া হেলেস্পন্ট দ্বীপে নির্বাসিত করেন। সেখানে নির্বাসিত থাকিয়া তিনি ৭৩ বৎসর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। দেব-দেবীর অনস্তিত্ব বিষয়ে শিক্ষা প্রচার করিতেন বলিয়া দার্শনিক প্রোটাগোরাসের প্রাণদণ্ড হইয়াছিল।
সক্রেটিসের শিষ্যগণের মধ্যে প্লেটোর নাম সর্বপ্রসিদ্ধ। মুসলমানগণ ইহাকে ‘আফলাতুন’ বলিয়া থাকেন। সৃষ্টি সম্বন্ধে ইহার মতের সারমর্ম এই — পৃথিবী চিরদিন বিদ্যমান আছে; ইহা সেই মঙ্গলময়ের প্রতিরূপ মাত্র। ইহার অন্তর্গত ভূতসমূহ অনন্তকাল হইতেই পরিবর্তনশীল; পরিবর্তন প্রবাহে সৃষ্টিক্রিয়া সংসাধিত হইতেছে।
আরিস্টটল (খ্রী. পূ. ৩৮৪) –গ্রীসের উপনিবেশ স্টেজেরা নামক স্থানে আরিস্টটলের জন্ম হয়। সৃষ্টি প্রকরণ সম্বন্ধে তাঁহার মত এই –“কেবল স্বর্গ ও পৃথিবী বলিয়া নহে; চেতন, অচেতন সমস্ত বস্তুই অনন্তকাল হইতে পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে। এই বিশ্ব এক স্বর্গীয় আত্মার প্রতিরূপ। সেই আত্মা কখনও নিশ্চেষ্ট নহেন। তিনি শক্তি ও কার্য স্বরূপ; বিশ্বের গতি, সৃষ্টি এবং আকৃতির মূলে সেই স্বর্গীয় আত্মার প্রভাব চিরবিদ্যমান।” এই প্রসিদ্ধ দার্শনিকের মতে, “এই বিশ্ব আত্মার সৃষ্ট নহে; পরন্তু তাহা (আত্মা) হইতে উৎপন্ন। জাগতিক পদার্থ দশ প্রকার; যথা –দ্রব্য, পরিমাণ, গুণ, সম্বন্ধ, স্থান, সময়, অবস্থা, সামান্য, কার্য ও ভাব।” বলা বাহুল্য, এই কয়েকটি পদার্থের উপরই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় নির্ভর করিতেছে।
লেবনিজ (খ্রী. অ. ১৬৪৬) –ইনি জর্মন দর্শনের সৃষ্টিকর্তা বলিয়া কথিত হন। তিনি বলেন, “মন ও শরীরের কার্য, দুইটি স্বাধীনভাবে পরিচালিত কলের কার্য বলিয়া মনে করিতে হইবে। সেসকল পূর্বব্যবস্থাপিত একটি নিয়মানুসারে পরিচালিত হইতেছে। ব্যবস্থাপক ঈশ্বরও হইতে পারেন। কিন্তু তিনি নিয়ম করিয়া দিয়া গিয়াছেন মাত্র। এখন যে তিনি কোনো কাজ করাইতেছেন, তাহা বলা যায় না। পক্ষান্তরে হল্যাণ্ডের দার্শনিক স্পিনোজা ঈশ্বরকে ‘সর্বকারণকারণ বলিয়া স্বীকার করিতেন। দার্শনিকদের মধ্যে এরূপ বিপরীত মতবাদ আরও আছে। আরিস্টটল প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের মতে, “পৃথিবীর গতি নাই, পৃথিবী নিশ্চল ও সীমাবদ্ধ।” কিন্তু ব্রুনো ঘোষণা করেন, “পৃথিবী ঘূর্ণিত হইতেছে; বিশ্ব অসীম এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকাল ধরিয়া পরিবর্তন চলিয়াছে।”[৩]
সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ে পাশ্চাত্যের মাত্র কয়েকজন দার্শনিকের মতবাদসমূহের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল। ইহা ভিন্ন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের শত শত দার্শনিকের শত শত মতবাদ দৃষ্ট হয়। উহাতে কোথায়ও আছে একাধিক দার্শনিকের মতের মিল, আবার কোথায়ও গরমিল, হয়তোবা বৈপরীত্যও। তথাপি অধিকাংশ দার্শনিকের একটি শেষ সিদ্ধান্ত আছে। তাহা এই — “এক অনাদি, অনন্ত, গরীয়ান ‘সৎ’ নিজেকে নানাভাবে ব্যক্ত করিতেছে– মানুষের দেহে, মনে, সমাজে, তাহার দীর্ঘ ইতিহাসে, জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, বৃক্ষে, লতায়, পুষ্পে; সুন্দর-অসুন্দর এবং সৎ অসৎ ব্যাপিয়া সে আত্মপ্রকাশ করিতেছে; আর মানুষের মনেও সেই প্রকাশের মহিমা ধ্যান করিবার মতো শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছে। এই সৎ এক এবং অদ্বিতীয়; বহুধা ব্যক্ত, কতক ব্যক্ত এবং কতক অব্যক্ত।”
————
[৩. পৃথিবীর ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ৫৬–৬৬।]
০৪. সৃষ্টিবাদ ও বিবর্তনবাদ
সৃষ্টিবাদ ও বিবর্তনবাদ
সৃষ্টিতত্ত্ব জানার কৌতূহলটি মানব মনে বহুদিনের পুরাতন। এই কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য মানুষ বহু মতবাদের জন্ম দিয়াছে। তবে সেই সমস্ত মতবাদকে সাধারণত চারিটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা –আদিম মত, ধর্মীয় মত, দার্শনিক মত ও বৈজ্ঞানিক মত। এই কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। তাহার মধ্যে আদিম জাতিদের মত, ধর্মীয় মত ও দার্শনিক মতবাদের কিছু কিছু আলোচনা এযাবত করা হইয়াছে। উহাতে দেখা গিয়াছে যে, আদিম ও ধর্মীয় মতবাদের প্রায় সব ক্ষেত্রেই এক এক জন সৃষ্টিকর্তা ছিলেন এবং তাঁহারা ছিলেন কোথায়ও ঈশ্বর, কোথায়ও দেবতা, কোথায়ও পশু-পাখি, এমনকি কোথায়ওবা পতঙ্গ। সেই সকল সৃষ্টিকর্তাদের স্বরূপ যাহাই হউক না কেন, সকল মতবাদের আসল রূপ একটিই। বর্তমান জগতটিকে আমরা যেরূপ দেখিতে পাইতেছি, ইহা সেই রূপেই সৃষ্টি করা হইয়াছিল এবং যত রকম গাছপালা ও জীব-জানোয়ার দেখিতেছি, সৃষ্টিকর্তা উহার প্রত্যেকটিকে এই রূপেই সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কাহারও ‘জাতিগত রূপ’-এ কোনো পরিবর্তন বা নূতনত্ব নাই। ইহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ জাতিগত রূপ ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট বজায় রাখিয়া বংশবৃদ্ধি করিতেছে মাত্র। সাধারণত এইরূপ একটি ধারণা সকল ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। আর এই রকম ধারণাকে বলা হয় সৃষ্টিবাদ। জড় কিংবা জীবজগতে এক-এর রূপান্তরে বহু’র উৎপত্তি– এইরূপ ধারণাকে বলা হয় অভিব্যক্তিবাদ বা বিবর্তনবাদ।
পূর্বে আলোচিত আদিম জাতিসমূহের ও বেদ-বাইবেলাদির সৃষ্টিতত্ত্বসমূহ সৃষ্টিবাদ-এর অন্তর্ভুক্ত এবং সামান্য মতানৈক্য থাকিলেও জগতের যাবতীয় ধর্মীয় মতবাদই সৃষ্টিবাদের আওতাভুক্ত। জগত ও জীবন সৃষ্টি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের সর্বস্বীকৃত যে মত, তাহাই অভিব্যক্তিবাদ বা বিবর্তনবাদ। দার্শনিকগণ সকলে না হইলেও বেশির ভাগই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে বিবর্তনবাদী। এই বিষয়ে একজন আধুনিক দার্শনিকের মতবাদের উল্লেখ করিতেছি। তিনি বলেন —
“সৃষ্টিবাদ অনুসারে জগতের একজন স্রষ্টা আছে। সাধারণত ঈশ্বরকেই জগতের স্রষ্টা বলা হয়; কিন্তু যারা ঈশ্বরবিশ্বাসী নন, এমন লেখকেরা প্রকৃতিকে জগতের উৎস বলে মনে করেন। যেমন, মিল (Mill)-এর মতে ঈশ্বর বলে কেউ নেই।“
“প্রকৃতি থেকেই জগতের সৃষ্টি। এমন এক সময় ছিল যখন জগতের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ঈশ্বর বা প্রকৃতি কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে জগত সৃষ্টি করেছিল। যাবতীয় বস্তু এবং জীব জগতসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সৃষ্ট হয়েছে। গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, বিভিন্ন ধরণের উদ্ভিদ এবং প্রাণীতে পূর্ণ এই জগত প্রথমে যেভাবে সৃষ্ট হয়েছিল, আজও ঠিক একইভাবে বর্তমান। মূলত এর রূপ বিন্দুমাত্রও পরিবর্তিত হয়নি।
“ঈশ্বরবিশ্বাসী সৃষ্টিবাদের দুইটি রূপ আছে। যথা –ক. নিরপেক্ষ সৃষ্টিবাদ (Theory of Absolute Creation) 978 3. 129Tapa lama (Theory of Dependent or Conditional Creation)।
“ক. নিরপেক্ষ সৃষ্টিবাদ –এ মতবাদ অনুসারে নিছক শূন্য (nothing) থেকে ঈশ্বরের দ্বারা এই জগত সৃষ্ট হয়েছিল। এমন এক সময় ছিল, যখন এই জগতের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। ঈশ্বর হলেন সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী এক শাশ্বত সনাতন পুরুষ। তিনি হলেন পূর্ণ; সেই কারণে এই জগতের কোনো প্রয়োজন তার ছিল না। কিন্তু তবু তার ইচ্ছা হলো, এক জগতের সৃষ্টি হোক। অমনি সঙ্গে সঙ্গেই জগতের সৃষ্টি হলো। জগত সৃষ্ট হবার পর ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টি প্রাকৃতিক শক্তির উপরই জগতকে ছেড়ে দিলেন। এই প্রাকৃতিক শক্তিই জগতকে নিয়ন্ত্রিত ও চালিত করতে লাগল। ঈশ্বর এই জগতের প্রথম বা মুখ্য কারণ (first cause)। এই প্রাকৃতিক শক্তিগুলি হলো দ্বিতীয় বা গৌণ কারণ (second cause)। জগত সৃষ্ট হবার পর ঈশ্বর জগতের বাইরে অবস্থান করেন এবং প্রয়োজন হলে জগতের পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করেন। এই মতবাদ অনুসারে জগতকে আমরা বর্তমানে যেভাবে বা যে রূপে দেখছি, জগত সেইভাবে সৃষ্ট হয়েছিল। জগত কোনোরূপ ক্রমবিকাশ বা বিবর্তনের ফলে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়নি।
“খ. সাপেক্ষ সৃষ্টিবাদ –এই মতানুযায়ী ঈশ্বর নিছক শূন্য থেকেই এই জগত সৃষ্টি করেন নি, জড়ের (matter) থেকে তিনি এই জগত সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বরের মতো জড় নিত্য ও অবিনাশী; জগত সৃষ্ট হবার পূর্বেই জড়ের অস্তিত্ব ছিল। এই জড়ের কোনো আকার ছিল না, এই জড় এলোমেলো এবং বিশৃঙখল অবস্থায় ছিল। ঈশ্বর এই জড়োপাদানকে একটা নির্দিষ্ট আকার দিলেন এবং এই বিশৃঙ্খল এলোমেলো উপাদানের মধ্যে শৃঙ্খলা এনে এই সুন্দর জগত সৃষ্টি করলেন। ভারতীয় দর্শনেও আমরা এই জাতীয় সাপেক্ষ সৃষ্টিবাদের দেখা পাই। বৈশেষিক দার্শনিকদের মতে, ঈশ্বর ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুতের নিত্য পরমাণুগুলির সাহায্যে এই জগত সৃষ্টি করেছেন। যে কোনো সৃষ্টির ক্ষেত্রে দুটি কারণ থাকে –একটি নিমিত্ত কারণ, আর একটি উপাদান। কারণ। জগতসৃষ্টির মূলেও এই দু’প্রকার কারণ ছিল। ঈশ্বর হলেন নিমিত্ত কারণ, জড় হলো উপাদান কারণ।
“পূর্বোক্ত উভয় প্রকার সৃষ্টিবাদে নিম্নলিখিত বৈশিষ্টগুলি পাওয়া যায় —
“অনন্তকাল ধরে ঈশ্বর এই জগত ছাড়া একাকীই ছিলেন। যেহেতু তিনি পূর্ণ, সেহেতু জগতের কোনো প্রয়োজন ছিল না। হয় নিছক শূন্য থেকেই, নতুবা পূর্বস্থিত জড়কেই উপাদানরূপে গ্রহণ করে তিনি এই জগত সৃষ্টি করেছেন। কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে খেয়ালবশত ঈশ্বর এই জগত সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির পর এই জগত ঈশ্বরের পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী চলতে থাকে। কেবলমাত্র প্রয়োজনবোধে অর্থাৎ জাগতিক ব্যাপারে যখন কোনো বিপর্যয় দেখা দেয়, তখনই ঈশ্বর জগতের কাজে হস্তক্ষেপ করেন। ঈশ্বর জগতের অভ্যন্তরে বিরাজ করেন না, জগতের বাহিরেই অবস্থান করেন। ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক বাহ্য সম্পর্ক (external relation), আন্তর সম্পর্ক (internal relation) নয়।”
উপরোক্ত মতবাদের সমালোচনায় তিনি বলেন —
“পূর্বোক্ত সৃষ্টিবাদ গ্রহণযোগ্য মতবাদ নয়। এই মতবাদ বিজ্ঞানের দ্বারাও সমর্থিত নয়। এই মতবাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগগুলি আনা যেতে পারে —
“প্রথমত এই মতবাদ অনুসারে ঈশ্বর পূর্ণপুরুষ— তার জগতের কোনো প্রয়োজন ছিল না। তবে তিনি এই জগত সৃষ্টি করলেন কেন? কোনো অভাববোধ থেকে এই জগত সৃষ্ট হতে পারে না, কারণ পূর্ণপুরুষের কোনো অভাবের প্রশ্ন ওঠে না। যদি বলা যায়, জীবের উপর করুণাবশত তিনি এই জগত সৃষ্টি করেছেন– তাহলেও প্রশ্ন থেকে যায়, এরই বা কি প্রয়োজন থাকতে পারে? সৃষ্টিবাদীরা এর কোনো সদুত্তর দেন না।
“দ্বিতীয়ত ঈশ্বর অন্য জগত সৃষ্টি না করে এই জগত সৃষ্টি করলেন কেন? ঈশ্বরের জগতের প্রয়োজন ছিল না –একথা বলাও যুক্তিযুক্ত নয়, কেননা জগতসৃষ্টির মাধ্যমে প্রকাশিত না হলে। জীবনের পক্ষে ঈশ্বরের সত্তাকে অনুভব করা সম্ভব নয়।
“তৃতীয়ত নিছক শূন্য (nothing) থেকে জগত সৃষ্টি করা ঈশ্বরের পক্ষেও সম্ভব নয়, কেননা শূন্য থেকে শূন্যই পাওয়া যায়। অসৎ থেকে সৎ-এর সৃষ্টি কিভাবে সম্ভব? যদি ধরে নেওয়া যায়। যে, ঈশ্বর নিছক শূন্য থেকে জগত সৃষ্টি করেছেন, তাহলে জগতও নিছক শূন্য হবে; যেহেতু কার্য কারণেরই পরিণাম। কারণে যা থাকে, তাই কার্যে পরিণত হয়। আবার যদি বলা যায় যে, ঈশ্বর পূর্বস্থিত জড় থেকেই এই জগত সৃষ্টি করেছেন, তাহলে এই জড়ের অস্তিত্ব ঈশ্বরকে সীমিত করবে, কিন্তু ঈশ্বরকে বলা হয়েছে অসীম ও অনন্ত, তার কোনো সীমা থাকতে পারে না।
“চতুর্থত ঈশ্বর কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে জগত সৃষ্টি করলেন কেন? তার পূর্বে বা পরে কেন জগত সৃষ্টি করলেন না? সৃষ্টিবাদীরা এই সব প্রশ্নের উত্তর দেন নি। তা ছাড়া অনন্তকালের কোনো এক বিশেষ মুহূর্তে ঈশ্বর জগত সৃষ্টি করেছেন –এ যদি স্বীকার করা যায়, তাহলে জগত সৃষ্টির পূর্বেও কালের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। কিন্তু জগত ছাড়া অর্থাৎ কোনো ঘটনা ছাড়া শূন্যগর্ভ কালের অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না।
“পঞ্চমত জগত সৃষ্টির পর ঈশ্বর যদি জগতের বাইরে অবস্থান করেন অর্থাৎ কিনা এই জগত যদি ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কবিযুক্ত হয়ে অবস্থান করে, তাহলে এই স্বতন্ত্র জগতের সত্তা ঈশ্বরকে সীমিত করবে এবং সে ক্ষেত্রে ঈশ্বরকে সসীম বলা যাবে।
“যষ্ঠত জগতের মধ্যে যদি বিপর্যয় দেখা দেয় বা জগত যদি ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট পথে না চলে, তাহলে প্রয়োজনবোধে ঈশ্বর জগতের কার্যে হস্তক্ষেপ করেন— এ মতবাদও গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা তাহলে ধারণা করতে হয় যে, ঈশ্বর নিখুঁত শিল্পী নন এবং ঈশ্বরের জগতসৃষ্টির মধ্যে নৈপুণ্যের অভাব ছিল। তা ছাড়া জগতের অমজননক বিষয় ও ঘটনাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে : যদি জগতের উপাদান এড়ই অমওঃ লর কারণ হয়, তাহলে ধারণা করতে হবে যে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপাদানের দোয়ত্রুটি দূর করার সামর্থ নেই; কিন্তু এ জাতীয় ধারণা ঈশ্বরের ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
“সপ্তমত সৃষ্টিবাদ অনুসারে ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের সম্পর্ক বাহ্য সম্পর্ক (external relation), কিন্তু এ মত স্বীকার করা যায়না। ঈশ্বর জগতের কারণ বলার অর্থ, জগতের মধ্য দিয়েই ঈশ্বরের প্রকাশ বা ঈশ্বরের সত্তা জগতের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে, জগতের সম্পর্ক আন্তর সম্পর্ক (internal relation)।
“সবশেষে, এই মতবাদে ঈশ্বরকে মানুষ বা সাধারণ কারিগরের মতো কল্পনা করা হয়েছে। কোনোমতেই যুক্তিসঙ্গত নয়।
“সুতরাং, সৃষ্টিবাদ গ্রহণযোগ্য মতবাদ নয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ এই জগতের গঠন ও ইতিহাস সম্পর্কে গভীরভাবে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, একটি সহজ সরল অবস্থা থেকে ক্রমে ক্রমে পরিবর্তিত হয়ে জগত আজকের এই জটিল অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। সুতরাং বিজ্ঞানের দ্বারা সমর্থিত এই অভিব্যক্তিবাদ বা বিবর্তনবাদই গ্রহণযোগ্য মতবাদ।” এখন আমরা সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মতবাদ বা বিবর্তনবাদ-এর কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব, প্রথম পদার্থ ও পরে জীব বিষয়ে।
০৫. বিজ্ঞান মতে সৃষ্টিতত্ত্ব (পদার্থ বিষয়ক)
বিজ্ঞান মতে সৃষ্টিতত্ত্ব
পদার্থ বিষয়ক
দেখা যায় –সনাতন ধর্মীয় সৃষ্টিতত্বে কোথায়ও কার্যকারণ সম্পর্কের ধারা বজায় নাই এবং জীব বা জড় পদার্থ, ইহাদের কোনো কিছু সৃষ্টির জন্য কোনো উপাদানের উল্লেখ নাই, আছে শুধু ব্যবহার। উহা যেন পূর্ব হইতেই প্রস্তুত ছিল। সৃষ্টিতত্ত্বের ধর্মীয় ব্যাখ্যায় যুক্তির কোনো স্থান নাই। কার্যকারণ সম্পর্ক বজায় রাখিয়া যুক্তির সাহায্যে জগতের প্রত্যেকটি ঘটনা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিল দর্শন। পরবর্তীকালে দর্শনশাস্ত্রের কার্যকারণ সম্পর্ক ও যুক্তিসমূহের উপর ভিত্তি করিয়া প্রমাণসহ জাগতিক ঘটনা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিল বিজ্ঞান।
সৃষ্টিতত্ত্বের ধর্মীয় মতবাদের অনেকটাই আজ বিজ্ঞানের কাছে অবান্তর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। “পৃথিবী চ্যাপ্টা নহে, গোল” –ইহা এখন সর্ববাদীসম্মত সত্য। “পূর্ব হইতে সূর্যের পশ্চিম দিকে গতি কোনো স্বর্গীয় দূতের টানাটানিতে হয় না, উহা হয় পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে” –ইহা এখন পাঠশালার শিশুরাও জানে। “পৃথিবী মাছ, গরু বা জলের উপর অবস্থিত নহে এবং চন্দ্র, সূর্য ও তারকারা ছাদ-আকৃতি আসমানে লটকানোও নহে; উহারা সকলেই শূন্যে অবস্থিত” –ইহা অবিশ্বাস করিবার মতো লোক এখন দুনিয়ায় অল্পই আছে।
সৃষ্টিতত্ত্বে বিজ্ঞানের এলাকা সুবিশাল। ধর্ম যেমন এক কথায়, গ্রন্থের কয়েক পঙক্তি বা পৃষ্ঠায়। বিশ্বের যাবতীয় সৃষ্টিতত্ত্ব সাগ করিয়াছে, বিজ্ঞান তাহা পারে নাই। বিজ্ঞানের সৃষ্টিতত্ত্ব বহুশাখাবিশিষ্ট এবং প্রত্যেক শাখায় গ্রন্থরাজি অজস্র। যেমন –আকাশতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব, দেহতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, ভূণতত্ত্ব ইত্যাদি। উহার আলোচনাসমূহের বিষয়সূচী লিখাও দুই-চারিখানা পুস্তকে সম্ভব নহে। কাজেই আমরা শুধু উহার কয়েকটি বিষয়ের কিঞ্চিৎ আভাস দিতে চেষ্টা করিব।
.
# বিশ্বের বিশালতা
সনাতন ধর্মীয় মতে –পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত, যাবতীয় সৃষ্টির মধ্যে বৃহত্তম বস্তুপিণ্ড এবং মানুষ জীবকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, ঈশ্বরের শখের সৃষ্টি এক বিশেষ জীব। মানুষ ঈশ্বরের শখের সৃষ্টি এক বিশেষ জীব কি না, সেই আলোচনা পরে হইবে; এখন দেখা যাক– পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত ও বৃহত্তম পদার্থ কি না।
কোনো স্থানের কেন্দ্রবিন্দু ঠিক করিতে হইলে উহার পরিধি জানা দরকার। পরিধি নির্ধারণ না করিয়া কেন্দ্র নির্ধারণ অসম্ভব। কিন্তু ধর্মীয় মতবাদে বিশের পরিধি নির্ধারণ না করিয়াই পৃথিবীকে বিশ্বের কেন্দ্র বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে।
পৃথিবী সূর্য হইতে প্রায় ৯৩০ লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া এক গোলাকার (দুইদিকে ঈষৎ চাপা) কক্ষপথে ভ্রমণ করিতেছে এবং প্রায় একই সমান্তরালে কম-বেশি দূরে থাকিয়া আরো ১০টি গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। গ্রহদের এই আবর্তনক্ষেত্রকে বলা হয় সৌরজগত। সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত আছে সূর্য এবং সীমান্তে আছে ভালকান গ্রহ। পৃথিবী উহার কেন্দ্রেও নহে এবং সীমান্তেও নহে।
বুধ, শুক্র ও মঙ্গল গ্রহ ভিন্ন পৃথিবীর চেয়ে ছোট গ্রহ সৌরাকাশে আর নাই। পৃথিবীর ব্যাস মাত্র ৭,৯২৬ মাইল। কিন্তু ইউরেনাসের ব্যাস ৩০,৮৮০ মাইল, নেপচুনের ব্যাস ৩২,৮৪০ মাইল, শনির ব্যাস ৭৫,০৬০ মাইল এবং বৃহস্পতির ব্যাস ৮৮,৭০০ মাইল। পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য ওজনে ৩৩০ হাজার গুণ বেশি এবং আয়তনে প্রায় ১৩ লক্ষ গুণ বড়। সৌররাজ্যে পৃথিবী নেহায়েত ছোট জিনিষ এবং মহাকাশে ইহার দৃশ্যমান অস্তিত্বই নাই।
সৌরজগতের বাহিরে যে সকল জ্যোতিষ্ক দেখা যায়, উহাদের দূরত্ব এত বেশি যে, উহা লিখিয়া কোনো ভাষায় প্রকাশ করিতে হইলে মাইল বা ক্রোশে কুলায় না। তাই বিজ্ঞানীরা উহা হিসাব করেন আলোক বৎসরে। এক সেকেণ্ডে প্রায় ১৮৬ হাজার মাইল বেগে চলিয়া আলোকরশ্মি এক বৎসরে যতদূর পথ অতিক্রম করিতে পারে, বিজ্ঞানীরা তাহাকে বলেন ‘এক আলোক বৎসর। সৌরজগতের বাহিরের যে কোনো জ্যোতিষ্কের দূরত্ব নির্ণয় করিতে হইলে আলোক বৎসর ব্যবহার করিতে হয়। পৃথিবী হইতে সূর্যের দূরত্ব প্রায় ৯৩০ লক্ষ মাইল, সূর্য হইতে পৃথিবীতে আলো আসিতে সময় লাগে প্রায় ৮ মিনিট। কিন্তু মহাকাশের কোটি কোটি নক্ষত্রের মধ্যে সবচেয়ে কাছে অন্য যে নক্ষত্রটি আছে, তাহার আলো পৃথিবীতে আসিতেও সময় লাগে প্রায় ৪ বৎসর। মহাকাশে চারি আলোক বৎসরের কম দূরত্বে কোনোদিকে সূর্য ব্যতীত কোনো নক্ষত্রই নাই।
আজ পর্যন্ত মহাকাশে প্রায় ১০,০০০ কোটি নক্ষত্রের সন্ধান বিজ্ঞানীরা পাইয়াছেন। উক্তরূপ দূরে দূরে থাকিয়া ঐ সমস্ত নক্ষত্র যে বিশাল স্থান জুড়িয়া আছে, তাহাকে বলা হয় নক্ষত্র জগত। নক্ষত্ররা প্রত্যেকেই এক একটি সূর্য, কোনো কোনোটি মহাসূর্যও বটে। মহাকাশে এরূপ নক্ষত্রও আছে, যাহারা আমাদের সূর্য অপেক্ষা কোটি কোটি গুণ বড়।[৪]
আমাদের সূর্য যে নক্ষত্র জগতে অবস্থিত, সেই নক্ষত্র জগতটি আবর্তিত হইতেছে। আমাদের সৌরজগতটি এই নক্ষত্র জগতের কেন্দ্র হইতে প্রায় ৩০ হাজার আলোক বৎসর দূরে থাকিয়া প্রতি। সেকেণ্ডে প্রায় ১৭৫ মাইল বেগে নক্ষত্র জগতের কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। একবার প্রদক্ষিণ করিতে সময় লাগে প্রায় ২২২ কোটি বৎসর। আমাদের এই সৌরজগতটিও নক্ষত্র জগতের কেন্দ্রে নহে।[৫]
নক্ষত্র জগতকে সুদূর হইতে দেখিলে উহার নক্ষত্রগুলিকে ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায় না, সমস্ত নক্ষত্র মিলিয়া একটি ঝাপসা আলো বা মেঘের মতো দেখায়। ঐ রকম মেঘকে নীহারিকা বলা হয়। (ইহা ভিন্ন আর এক জাতীয় নীহারিকা আছে, উহারা শুধু বাম্পময়)। বিজ্ঞানীরা এই পর্যন্ত প্রায় ১০ কোটি নীহারিকা বা নক্ষত্র জগতের সন্ধান পাইয়াছেন এবং সবগুলি নীহারিকা মিলিয়া যে পরিমাণ স্থান জুড়িয়া আছে, তাহাকে বলেন নীহারিকা জগত বা ‘বিশ্ব। আমাদের নক্ষত্র জগত বা নীহারিকাটি যে বিশ্বের কেন্দ্রে অবস্থিত, এমন কথাও বলা যায় না। এই বিশ্ব এতই বিশাল যে, ইহার এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তের দূরত্ব অর্থাৎ ব্যাস প্রায় ৪,০০০ কোটি আলোক বর্ষ।[৬] বিজ্ঞানীপ্রবর আইনস্টাইন বলেন যে, নীহারিকা জগত বা বিশ্ব ক্রমশ প্রসারিত হইতেছে।
বিশ্বের আয়তনের বিশালতা আমরা শুধু কথায় বা লেখায়ই প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু ধারণায় আনিতে পারি না। এই কল্পনাতীত বিশ্ব এমনই বিশাল যে, জীবসমাকুল পৃথিবী, গ্রহসমাকুল সৌরজগত, এমনকি সৌরসমাকুল নক্ষত্র জগত পর্যন্ত ইহার মধ্যে হারাইয়া যায়। অর্থাৎ বিশ্বে এমনও স্থান আছে, যেখান হইতে চাহিলে আমাদের পৃথিবী, সূর্য, এমনকি বিশাল নক্ষত্র জগতও অদৃশ্য হইয়া পড়ে।
.
# বিশ্বের আকৃতি
এককালে মানুষের ধারণা ছিল যে, পৃথিবী থালার মতো গোল ও চ্যাপ্টা এবং ইহার চতুর্দিকে প্রাচীর বা পর্বত দ্বারা ঘেরাও করা। সেই প্রাচীর বা পর্বতের নাম কোহেক্বাফ। কোহেকৃাফের বহির্ভাগে কি আছে না আছে, কোনো মানুষ তাহা জানে না। তখন স্থির হইয়াছিল যে, পৃথিবীর উপরে আছে আসমানি ছাদ এবং সীমান্তে কোহেক্বাফ। কিন্তু নিচে? কেহ বলিলেন, পৃথিবীর নিচে জল, কেহ বলিলেন মাছ; এইরূপ কেহ গরু, কেহ কচ্ছপ ইত্যাদি বলিলেন। এই সব অলীক কল্পনার জন্য উহাদের নিন্দা করা যায় না। কেননা সেই যুগের মানুষ হইলে আমরা কি বলিতাম? হয়তো ঐরূপই কিছু। আর তাহারা যদি এই যুগের মানুষ হইতেন এবং ভূগোল খগোল পাঠ করিতেন, তবে তাহারাও বলিতেন, “পৃথিবী কমলালেবুর মতো গোল এবং শূন্যে থাকিয়া নিজে নিজে ঘুরপাক খায় ও নিয়ত সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে; অধিকন্তু পৃথিবীর ন্যায় আরও ১০টি গ্রহ আছে, উহারাও পৃথিবীর মতো সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরপাক খায়।”
সেকালে এই গোটা পৃথিবীটিকেই বলা হইত জগত। এখন দেখা যাইতেছে যে, জগত একটি নহে, অনেক। যেমন –সৌরজগত, নক্ষত্র জগত, নীহারিকা জগত ইত্যাদি। আর এই সকল জগতকে একত্রে বলা হয় বিশ্ব। এখন প্রশ্ন হইল এই যে, এই বিশ্বের আকৃতি কিরূপ?
আমরা যে নক্ষত্র জগতে বাস করি, এই জগতটির আকৃতি গোল অথচ চ্যাপ্টা, কতকটা ডাক্তারদের ট্যাবলেট-এর মতো। আমাদের পৃথিবী উত্তর-দক্ষিণে চাপা, অর্থাৎ ইহার বিষুবীয় অঞ্চলের ব্যাস ৭,৯২৬ মাইল ও মেরু অঞ্চলের ব্যাস ৭,৯০০ মাইল; ব্যবধান ২৬ মাইল মাত্র। আর আমাদের নক্ষত্র জগতটির বড় ব্যাস ১২০ হাজার আলোক বর্ষ এবং ছোট ব্যাস ২০ হাজার আলোক বর্ষ; ব্যবধান ১ লক্ষ আলোক বর্ষ।
প্রত্যেকটি নক্ষত্র জগত বা নীহারিকার মাঝখানের দূরত্ব লক্ষ লক্ষ আলোক বর্ষ। যে কোনো দুইটি নীহারিকার মাঝখানে যে স্থান, সেখানে তাপ নাই, চাপ নাই, আলো নাই; অর্থাৎ কোনো পদার্থই নাই। উহা চিরঅন্ধকার, চিরশীতল, বিশাল মহাশূন্য! মতান্তরে –বস্তুশূন্য কোনো স্থান নাই। কেননা সমস্ত বিশ্বব্যাপী ইথর বিদ্যমান এবং উহা একটি পদার্থ।[৭]
নীহারিকাগুলি পরস্পর দূরে সরিয়া যাইতেছে এবং নীহারিকা বিশ্বটি ক্রমশ স্ফীত হইতেছে। বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, আমাদের নক্ষত্র জগত হইতে যে নীহারিকার দূরত্ব যত বেশি, সেই নীহারিকার দূরে সরিয়া যাওয়ার বেগও তত বেশি। প্রতি এক লক্ষ আলোকবর্ষ দূরত্ব বৃদ্ধিতে প্রতি সেকেণ্ড ১০০ মাইল বেগ বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে সবচেয়ে দূরের নীহারিকার দূরে সরিয়া যাওয়ার বেগ আলোর বেগের ৯/১০; অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ড ১,৬৭,৪০০ মাইল। নীহারিকাগুলি কত যুগ-যুগান্ত হইতে এইরূপ প্রচণ্ড বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই এবং কোনো কালেও যে উহারা কোনো সীমান্তে পৌঁছিবে– বিজ্ঞানীগণ আজ পর্যন্ত তাহারও কোনো হদিস পান না।
আর একটি কথা এই যে, আমরা যে পৃথিবীটিতে আছি, তাহারই চতুষ্পর্শ্বে যে নক্ষত্র নীহারিকাগুলি ভীড় জমাইয়া আছে, এইরূপ মনে করিবার কোনো কারণ নাই। হয়তো এই বিশ্বের। অনুরূপ কোটি কোটি বিশ্ব লইয়া ‘মহাবিশ্ব গঠিত হইয়া থাকিবে। আবার কোটি কোটি মহাবিশ্ব লইয়া ‘পরমবিশ্ব’, অতঃপর ‘চরমবিশ্ব’ ইত্যাদি অনন্ত বিশ্ব থাকা বিচিত্র নহে।[৮] তাই বলিতে হয়, বিশ্ব অসীম। আর অসীমের কোনো আকৃতি থাকিতে পারে না। কাজেই বিশ্বের নির্দিষ্ট কোনো আকৃতি নাই।
.
# বিশ্বের উপাদান
জগতের যে কোনো পদার্থের উপাদানসমূহের পরিচয় জানিতে হইলে পদার্থটিকে ভাঙ্গা আবশ্যক। বিজ্ঞানীগণ জগতের বিবিধ পদার্থের মৌলিক উপাদান নির্ণয়ের জন্য জৈবাজৈব বহু পদার্থই ভাঙ্গিয়া দেখিয়াছেন। ইহাতে তাহারা ফল যাহা পাইয়াছেন, এইখানে তাহার কিছু আভাস দিতে চেষ্টা করিব।
প্রথমত, বিশ্বের একটি অংশ নীহারিকা, নীহারিকার অংশ নক্ষত্র বা সূর্য, সূর্যের অংশ গ্রহ এবং গ্রহের অংশ উপগ্রহ ইত্যাদি। আমাদের পৃথিবী একটি গ্রহ এবং ইহার একটি অংশ হিমালয় পর্বত। এই হিমালয়কে ভাঙ্গিলে পাওয়া যাইবে ক্রমে প্রস্তরখণ্ড, কত্তকর, শেষ পর্যন্ত ধূলিকণা। এই ধূলিকণাকে ক্রমাগত ভাগিতে থাকিলে পাওয়া যাইবে অণু।
জগতের কঠিন, তরল ও বায়বীয় যে কোনো পদার্থ ভাঙ্গিয়া পাওয়া যায় এই অণু। এই অণুর পর্যায়ে পৌঁছা পর্যন্ত পদার্থের পূর্ব গুণাগুণ বজায় থাকে। অণু এত ছোট যে, খালি চোখে উহা দেখা যায় না। একটি অণুর ব্যাস এক সেন্টিমিটারের পাঁচ কোটি ভাগের এক ভাগের সমান। একটি ক্ষুদ্র জলকণাকে যদি পৃথিবী বলিয়া মনে করা হয়, তবে একটি অণু হইবে একটি ফুটবলের সমান। বিজ্ঞানী অ্যাস্টন বলেন, “এক গ্লাস জলের প্রতিটি অণুর গায়ে লেবেল আঁটিয়া অর্থাৎ চিহ্নিত করিয়া ঐ জল যদি পৃথিবীর সাগর, মহাসাগর, নদী ও পুকুরাদির যাবতীয় জলের সহিত ভালোরূপে মিশাইয়া দেওয়া যায় এবং মিশ্রিত জল হইতে এক গ্লাস জল তোলা হয়, তবে এই এক গ্লাস জলে চিহ্নিত অণুর সংখ্যা থাকিবে অন্তত দুই হাজার।”
জগতের বস্তুসমূহের রূপ-গুণের যে বৈচিত্র, তাহা এই অণুর পর্যায়ে আসিয়াই শেষ হইয়া যায়। বিজ্ঞানীগণ বিবিধ কৌশলে এই অণুকে ভাঙ্গিয়াছেন এবং অণুকে ভাঙ্গিয়া যাহা পাইয়াছেন, তাহাকে বলা হয় পরমাণু বা অ্যাটম। যে সকল পদার্থ অণুর পর্যায় পর্যন্ত স্বধর্ম বজায় রাখিতে পারে এবং তৎপরে হারাইয়া ফেলে, তাহাদের বলা হয় যৌগিক ও যে সকল পদার্থ পরমাণুর পর্যায় পর্যন্ত স্বধর্ম বজায় রাখিতে পারে, তাহাদের বলা হয় মৌলিক পদার্থ।
তুঁতে ও লবণ দুইটি যৌগিক পদার্থ। ইহাদের অণুকে ভাঙ্গিলে কাহারও নিজ নিজ রূপগুণ বজায় থাকে না। অঁতের অণুকে ভাঙ্গিলে পাওয়া যায় তামা, গন্ধক ও অক্সিজেন নামক বায়বীয় পদার্থের পরমাণু এবং লবণের অণুকে ভাঙ্গিলে পাওয়া যায় সোডিয়াম ও ক্লোরিন নামক পদার্থের পরমাণু। সুতরাং পুঁতে ও লবণ যৌগিক পদার্থ এবং তামা, গন্ধক, অক্সিজেন, সোডিয়াম ও ক্লোরিন মৌলিক পদার্থ। কোনো যৌগিক পদার্থের অণুকে ভাঙ্গিলে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণু পাওয়া যায়, কিন্তু মৌলিক পদার্থের অণুকে ভাগিলে অন্য কিছুই পাওয়া যায় না। যেমন স্বর্ণ একটি মৌলিক পদার্থ। উহার অণুকে ভাঙ্গিলে স্বর্ণ পাওয়া যায়, অন্য কিছু নহে। প্রকৃতিতে স্বভাবত যে সকল যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয়, তাহার সংখ্যা প্রায় ৪ লক্ষ। কিন্তু মৌলিক পদার্থের সংখ্যা বেশি নহে।
ধর্মগুরুরা সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহার উপাদান লইয়া মাথা ঘামান নাই। এই বিষয়ে দার্শনিকেরাই প্রথম আরম্ভ করেন জগতসৃষ্টির উপাদানসমূহের খোঁজ-খবর লইতে। আদিতে দার্শনিকদের কাছে মৌলিক পদার্থের সংখ্যা ছিল ৪টি। যথা –জল, অগ্নি, মৃত্তিকা ও বায়ু; অর্থাৎ আব, আতস, খাক, বাত। প্রাথমিক স্তরের বিজ্ঞানীদের কাছে ছিল স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র ও পারদাদি ৮টি মৌলিক পদার্থ বা ধাতু। বিজ্ঞানের উৎকর্যের সাথে সাথে নূতন নূতন মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হইতে থাকে এবং ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে ইউরেনিয়াম আবিষ্কৃত হইলে ধাতুর সংখ্যা দাঁড়ায় ৯২টি। ১৯৪০ সালে নেপচুনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম নামক দুইটি ধাতু আবিষ্কৃত হয় এবং পর পর ১৯৫৭ সালের মধ্যে আরও ৮টি ধাতু আবিষ্কৃত হয়। সর্বশেষ ধাতুটির নাম রাখা হইয়াছে নোবেলিয়াম। বিজ্ঞানীগণ কোনো কোনো সূত্রের সাহায্যে জানিতে পারেন যে, সম্ভবত অজানা ধাতু আরও দুইটি আছে। সে যাহা হউক, অধুনাতন ধাতুর সংখ্যা ১০২টি। আলোচ্য মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের বিভিন্ন অনুপাত ও বিভিন্ন কৌশলে সংযোজনার ফলে উদ্ভূত হইয়াছে জগতের যাবতীয় সৃষ্টিবৈচিত্র।
১০২টি মৌলিক পদার্থের মধ্যে অধিকাংশই কঠিন, কিছুসংখ্যক বায়বীয় এবং অল্পসংখ্যক তরল। যেমন –সোনা, রূপা, লোহা, তামা, শীশা ইত্যাদি কঠিন; হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, হিলিয়াম ইত্যাদি বায়বীয় এবং পারদাদি তরল। ইহার মধ্যে কতক সহজ ও স্বাভাবিকভাবে মিশিয়া যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে। যেমন –হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিশিয়া জল এবং অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বনাদি মিশিয়া বাতাস সৃষ্টি করে। ইহাদিগকে বলা হয় প্রাকৃতিক যৌগিক পদার্থ।
কতগুলি মৌলিক পদার্থ আছে, তাহারা একে অন্যের সহিত সহজে মিশিতে চায় না। বিজ্ঞানীগণ রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক নানা উপায়ে উহাদিগকে মিশাইয়া নানাবিধ কৃত্রিম যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করেন। যেমন –পিতল, কাসা, কঁচ, প্লাস্টিক, বিবিধ রং ইত্যাদি। আজকাল পৃথিবীর আনাচে-কানাচে বিশেষত বাজারে কৃত্রিম যৌগিক পদার্থের তৈয়ারী মালামালের এতই ছড়াছড়ি যে, কোনো ব্যক্তির পক্ষে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।
বিজ্ঞানীদের রসায়নাগারে কৃত্রিম উপায়ে প্রাকৃতিক যৌগিক পদার্থ যে তৈয়ারী হইতেছে না। তাহা নহে। বাতাসের নাইট্রোজেন ও জলের হাইড্রোজেনকে বেশি উষ্ণতায় ও প্রচণ্ড চাপে রাসায়নিক মিলনে অ্যামোনিয়ায় পরিণত করা হয় এবং এই অ্যামোনিয়া হইতে প্রস্তুত হয় সোরা।
এক একটি পরমাণু যে কত ছোট, তাহা কল্পনায় আনা যায় না এবং সংখ্যা দ্বারা লিখিতে পারিলেও উহার পাঠোদ্ধার করা যায় না। উদাহরণস্বরূপ দেখান যাইতে পারে যে, একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন এ্যাম হিসাবে লিখিতে হইলে উহাতে দশমিক বিন্দুর ডানদিকে ২৪টি শূন্য বসাইয়া ১৭ সংখ্যাটি বসাইতে হয়।
যথা–.০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০১৭ গ্রাম।[৯]
এই কল্পনাতীত ক্ষুদ্র পরমাণুকেও বিজ্ঞানীগণ ভাঙ্গিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং পরমাণুর গর্ভে পাইয়াছেন কয়েকটি শক্তিকণিকা। তাহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, পজিট্রন, মিসোটুন, নিউট্রিনো ইত্যাদি।
বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, প্রকৃতির রূপবৈচিত্রে যতই তারতম্য থাকুক না কেন, উহাদের মৌলিক উপাদান একই। অর্থাৎ ইলেকট্রন-প্রোটনাদি শক্তিকণিকা। তারতম্য শুধু পরমাণুগর্ভে ইলেকট্রন প্রোটনাদির সংখ্যায়।
বিজ্ঞানীগণ পদার্থের পরমাণু ভাঙ্গিয়া যে সব শক্তিকণিকা পাইয়াছেন, এক কথায় উহাকে বলা হয় তড়িৎ বা বিদ্যুৎ। এই বিদ্যুৎশক্তি বর্তমান জগতের যে সকল পরিবর্তন সাধন করিয়াছে ও করিতেছে তাহা দেখিলে বা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। এই শক্তি শুধু টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বিজলিবাতি, রেডিও এবং নানাবিধ কল-কক্সা চালনায়ই সীমাবদ্ধ নহে; ইহা গোটা মানব জাতির শিক্ষা, সভ্যতা ও মানবতায় পরিবর্তন আনয়ন করিয়াছে।
বিজ্ঞানীগণ কয়েকটি উপায়ে জানিতে পারেন যে, বিশ্বের কোনো স্থানে ইলেকট্রনাদি ধ্বংস হইতেছে এবং তাহার ফলে এক মহাশক্তির জন্ম হইতেছে। তাই বিজ্ঞানীগণ ইলেকট্রনাদির বিনাশে শক্তি উৎপাদনের প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন এবং তাহাতে সাফল্য লাভ করেন। দেখা গিয়াছে যে, ইলেকট্রনাদি ধ্বংসে শক্তি উৎপন্ন হইতে পারে এবং শক্তি সংহর্ত হইয়া ইলেকট্রনাদির সৃষ্টি হইতে পারে। তাই বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের মৌলিক উপাদান শক্তি।
————
৪. খগোল পরিচয়, মো, আ, জব্বার, পৃ. ২৭।
৫. নক্ষত্র পরিচয়, প্রমথনাথ সেনগুপ্ত, পৃ. ১৪, ১৫।
৬, নক্ষত্র পরিচয়, প্রমথনাথ সেনগুপ্ত, পৃ. ১৬।
৭ খগোল পরিচয়, মো. আ, জব্বার, পৃ. ১১১, ১১২।
৮, জগত ও মহাজগত, এম, এ, জব্বার, পৃ. ৪৩।
৯. বিশ্বের উপাদান, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ. ৭।
০৬. সৃষ্টির ধারা
সৃষ্টির ধারা
আমাদের দেহ সসীম, মজ্জা সসীম, তাই জ্ঞানও সসীম। অসীম ও অনন্তকে আমরা কল্পনা করিতে পারি না। যেহেতু জীবনের যত সব কারবার আমাদের সসীমকে লইয়া। সসীম কল্পনায়ই আমরা অভ্যস্ত। পরম বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলিয়াছেন, “বিশ্ব সসীম অথচ অসীম”। মহাসমুদ্রের মাঝে দাঁড়াইয়া চাহিলে সমুদ্রকে মনে হয় অসীম। কিন্তু যে দ্বীপে বা জাহাজে দাঁড়াইয়া দেখা যায়, তাহাকে দেখা যায় সসীম। সেইরূপ গ্রহ-নক্ষত্র বা নীহারিকা জগতও সসীম। কিন্তু বিশ্ব সসীম নহে। বিশ্ব যেমন সীমাহীন, তেমনি আদি ও অন্তহীন। অনন্ত বিশ্বসাগরে গ্রহ, তারা ও নীহারিকাগুলি যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ মাত্র। ইহাদেরই আছে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়। বিজ্ঞানীগণ ইহাদেরই সৃষ্টি বিষয়ে আলোচনা করিয়া থাকেন, বিশ্ব সম্বন্ধে নহে। বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয় অর্থাৎ আদি ও অন্ত নাই, আছে শুধু স্থিতি।
সৃষ্টিতত্ত্ব নির্ণয়ের ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে সামান্য মতভেদ আছে। সেই মতভেদ উপেক্ষা করিয়া আমরা উহাদের মধ্যে বহুজন স্বীকৃত মতবাদ-এর ভিত্তিতে সৃষ্টিতত্ত্বের বর্ণনা করিব। বলা বাহুল্য যে, বিজ্ঞানীদের সকলের সকল মতবাদের মূল একই, অর্থাৎ বস্তুবাদ।
বিজ্ঞানীদের মতে –বর্ণনাতীত কালে অনন্ত বিশ্বের সর্বত্র বিরাজ করিত নিরাকার এক শক্তি বা তেজ। কালক্রমে তেজশক্তি রূপান্তরিত হয় তড়িৎশক্তিতে, যাহার পরিবাহক ইলেকট্রন প্রোটনাদি শক্তিকণিকা। ইহারা সম্পূর্ণ নিরাকার নহে এবং সাকারও নহে। ইহারা সাকার ও নিরাকারের মাঝামাঝি অর্থাৎ ইহারা পদার্থও নহে এবং অপদার্থও নহে। ইহারা সতত চঞ্চল ও গতিশীল।
কালক্রমে মহাশূন্যে ঐ সকল শক্তিকণিকা সংহত হয়, অর্থাৎ বিভিন্ন সংখ্যায় জোড় বাধিয়া যায়। ইহাতে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন ধরণের পরমাণুর। ইহারাও চঞ্চল ও গতিশীল। এই পরমাণুময় জগতটিই নীহারিকা জগত।
হয়তো অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন যে, জলা মাঠের কর্দম শুকাইতে থাকিলে মাটিতে ফাটল ধরে। কিন্তু কেন ধরে? জলসহ কাদামাটির যে আয়তন থাকে, মাটিস্থ জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাওয়ায় তাহার সে আয়তন থাকে না, কমিয়া যায়। কিন্তু মাঠের পরিধি কমে না। অর্থাৎ মাঠের প্রান্তসীমা ঠিকই থাকিয়া যায়। কাজেই ফাটলের মাধ্যমে জলের ঐ ঘাটতি পূরণ হয়। পক্ষান্তরে ইতস্তত ফাটলের যোগাযোগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্র উৎপন্ন হয় এবং ক্ষেত্রগুলির আকৃতিতে মোটামুটি সাদৃশ্য থাকে। কিন্তু আয়তন হয় বিভিন্ন।
উক্তরূপ — অখণ্ড নীহারিকা জগতের ইলেকট্রন ও প্রোটনাদি পরস্পর জোড় বাধিয়া সংহত হওয়ার ফলে হাইড্রোজেনাদি বায়বীয় পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং ইহাতে নীহারিকার আয়তন কমিবার দরুন স্থানে স্থানে ফাটলের সৃষ্টি হয়। ইহার ফলে অখণ্ড নীহারিকা জগত বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নীহারিকার উদ্ভব হয়।
কালক্রমে অন্যান্য মৌলিক পদার্থের ভারি পরমাণুগুলির সৃষ্টি হয় এবং খণ্ডিত নীহারিকার আয়তন আরো কমিতে থাকে। ইহার ফলে পরমাণুদের নৈকট্য বৃদ্ধি পায় এবং পরস্পর সংঘর্ষের ফলে নীহারিকা রাজ্যে সৃষ্টি হয় তাপ-এর।
কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও পরমাণুর গঠন সম্বন্ধে এইখানে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। পরমাণুদের গঠনোপাদান প্রধানত ইলেকট্রন ও প্রোটন; কিছু নিউট্রন, পজিট্রন, নিউট্রিনো এবং মিসোটুনও থাকে। কিন্তু উহারা এলোমেলোভাবে থাকে না, থাকে সুসংবদ্ধভাবে। পরমাণুর কেন্দ্রে। থাকে পজিটিভ বিদ্যুযুক্ত প্রোটন এবং বাহিরের বৃত্তাকার কক্ষে ভ্রমণ করে নেগেটিভ বিদ্যুৎযুক্ত ইলেকট্রন। ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যার উপর নির্ভর করে যাবতীয় মৌলিক পদার্থের রূপায়ণ। বাহিরে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে ভ্রমণরত ইলেকট্রনের সংখ্যা থাকে যত, কেন্দ্রে প্রোটনের সংখ্যা থাকে তত।
হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে একটি প্রোটন ও বাহিরের কক্ষে থাকে একটি মাত্র ইলেকট্রন। তাই বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের মধ্যে হাইড্রোজেনই বেশি হাল্কা। এই রকম ইলেকট্রন বা প্রোটনের সংখ্যা হিলিয়ামে ২, লিথিয়ামে ৩, বেরিলিয়ামে ৪; বরাবর যাইয়া সোনায় সংখ্যা দাঁড়ায় ৭৯, পারদে ৮০, ইউরেনিয়ামে ৯২ এবং নোবেলিয়ামে ১০২। এক একটি পরমাণু যেন এক একটি ছোট সৌরজগত। সূর্যকে কেন্দ্রে রাখিয়া যেমন গ্রহগণ ঘুরিতেছে, প্রোটনকে কেন্দ্রে রাখিয়া তেমন ইলেকট্রনরা প্রতি সেকেণ্ডে ১৩০০ মাইল বেগে ঘুরিতেছে।
একটি জলপূর্ণ পাত্রে কয়েক টুকরা শোলা বা অনুরূপ কিছু ঘুরাইয়া জলের উপর আলাদা আলাদাভাবে ছাড়িয়া দিলে দেখা যায় যে, উহারা জলের উপর ভাসিয়া পৃথক পৃথক ঘুরিতে থাকে এবং কোনো কৌশলে উহাদের পরস্পরকে সংলগ্ন করিয়া রাখিলে দেখা যায় যে, উহারা পৃথক থাকিয়া যে পাকে ঘুরিতেছিল, সমবেতভাবে এখন সেই একই পাকে ঘুরিতেছে। উক্তরূপ ঘূর্ণায়মান গতিবিশিষ্ট ইলেকট্রনে গঠিত পরমাণুরা হয় ঘূর্ণিগতিশীল এবং পরমাণুগঠিত নীহারিকারাজিও হয় ঘূর্ণায়মান ও গতিশীল।
কালক্রমে নীহারিকারাজি তাহাদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে আয়তনে ছোট হইতে থাকে এবং উহাতে তাহাদের তাপ ও ঘূর্ণিবেগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এইভাবে নীহারিকার তাপবৃদ্ধি হইয়া কয়েক লক্ষ বা কোটি ডিগ্রী হইলে উহারা হইয়া দাঁড়ায় এক একটি নক্ষত্র। তবে সকল নক্ষত্র সমান তাপ ও আয়তন বিশিষ্ট হয় না, উহাতে যথেষ্ট পার্থক্য থাকে।
প্রজ্জ্বলিত বাষ্পীয়দেহধারী নক্ষত্র বা সূর্যের আবর্তনবেগ অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইলে উহাদের কেন্দ্ৰাপসারণী শক্তির (centrifugal force) প্রভাবে নিরক্ষদেশ স্ফীত হইতে থাকে এবং মেরুদেশ চাপিয়া যায়। ক্রমসকোচনের ফলে কেন্দ্ৰাপসারণী শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং নিরক্ষদেশ হইতে অভগুরীয় আকারে খানিকটা অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। বিচ্ছিন্ন অংশও দূরে যাইয়া আবর্তিত হইতে থাকে এবং পরে উহাই হইয়া দাঁড়ায় এক একটি গ্রহ।
আমাদের সৌরজগতটিও একটি খণ্ড নীহারিকা মাত্র। ইহার আবর্তনবেগে (মতান্তরে অন্য কোনো নক্ষত্রের আকর্ষণে) ক্রমশ ১১টি অঙ্গুরীয় খসিয়া ১১টি গ্রহের সৃষ্টি হইয়াছে। এই এগারোটি গ্রহের মধ্যে একটি আমাদের এই পৃথিবী এবং অপর গ্রহসমূহ –বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো, পসিডন ও ভালকান (ইহাদের বিষয় পরে আলোচিত হইবে)। আমাদের সৌরজগতের ব্যাস প্রায় ৭৩৪ কোটি মাইল।
জ্বলন্ত সূর্যের বাষ্পীয় দেহ হইতে জন্ম লইবার সময় পৃথিবীও জ্বলন্ত দেহধারী ছিল এবং পৃথিবীর তাপমাত্রাও সূর্যের তাপমাত্রার সমান ছিল। বিশেষত আয়তনেও বর্তমানের তুলনায় বহুগুণ বড় ছিল। কালক্রমে তাপ ত্যাগ করিয়া পৃথিবীর দেহ সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং ভারি ধাতুর পরমাণুগুলি বায়বীয় অবস্থা ত্যাগ করিয়া তরল অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। যে সকল ধাতু অপেক্ষাকৃত ভারি, তাহা পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে এবং অপেক্ষাকৃত হাল্কা ধাতু-পদার্থগুলি উপরে থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্তরে সজ্জিত হয়।
ভূবিজ্ঞানীরা বলেন যে, ভূগর্ভে প্রধান স্তর তিনটি। প্রথম –ভূ-কেন্দ্র হইতে ‘তরল ধাতু স্তর’ ২২০০ মাইল, ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব (জলের তুলনায়) প্রায় ১১; দ্বিতীয়– ‘নমনীয় ব্যাসল্ট স্তর’ ১৮০০ মাইল, ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৮৬; তৃতীয় –‘কঠিন গ্রানাইট স্তর ৩০ মাইল, ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ২.৬৫। পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের গড় আপেক্ষিক গুরুত্ব ৫.৫২।[১০]
বর্তমানে ভূপৃষ্ঠের গড় উত্তাপ প্রায় ৬৮° ফারেনহাইট বা ২০° সেন্টিগ্রেড। কিন্তু ভূগর্ভের ৩০ মাইল নিচের উত্তাপ প্রায় ১২০০° সে. এবং কেন্দ্রীয় অঞ্চলের তাপমাত্রা ৬০০০° সে.। ইহা সূর্যের বহিরাবরণের তাপের সমান।[১১]
পৃথিবী সূর্যের প্রজ্জ্বলিত বাষ্পীয় দেহের স্খলিত অংশ হইতে জন্ম লইয়া ক্রমশ তাপ ত্যাগ করিয়া শীতল ও সঙ্কুচিত হইতে থাকে এবং ইহার ফলে পৃথিবীর আবর্তন (rotation) বেগ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আবর্তন বেগ বৃদ্ধির ফলে নিরক্ষদেশ স্ফীত ও মেরুদেশ চাপা হইতে থাকে। নিরক্ষদেশ অতিমাত্রায় স্ফীত হইলে, স্ফীত অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া (মতান্তরে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের গ্রানাইট স্তরের খানিকটা অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া) যায় এবং তাহা হইতে চন্দ্রের জন্ম হয়।
“কোনো গোলকের ব্যাস বা পরিধি এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব জানা থাকিলে, উহার ওজন নির্ণয় করা সম্ভব।” এই সূত্রটি অনুসারে বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীর ওজন নির্ণয় করিয়াছেন। উহা টনের হিসাবে লিখিতে হইলে ৬-এর ডানে ২১টি শূন্য বসাইতে হয়।
যথা –৬,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০, ০০০,০০০ টন।[১২]
পৃথিবীর পরিধি প্রায় ২৫ হাজার মাইল এবং ভূপৃষ্ঠের মোট আয়তন ১৯.৬৯ কোটি বর্গমাইল। ইহার মধ্যে জলভাগ ১৩.৯৪ এবং স্থলভাগ ৫.৭৫ কোটি বর্গমাইল। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের শতকরা ৭০.৭৮ ভাগ জল ও ২৯.২২ ভাগ স্থল।
কতিপয় ফল শুকাইলে যেমন তাহার পৃষ্ঠদেশ কুঁচকাইয়া যায়, অর্থাৎ উঁচুনিচু হইয়া নানাবিধ ভাঁজ পড়ে, তেমন পৃথিবী ক্রমশ শীতল ও সঙ্কুচিত হইয়া ভূপৃষ্ঠের গ্রানাইট স্তরে ভাঁজ পড়ে। কথাটি আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলি।
মনে করা যাক, একটি ফলের ত্বকের পরিধি হইল ৬ ইঞ্চি এবং তাহার মাংসল অংশের পরিধি ৫ ইঞ্চি। ঐ ফলটি শুকাইয়া তাহার মাংসল অংশের পরিধি হইল ৪ ইঞ্চি। কিন্তু উহার ত্বকের পরিধি বিশেষ কমিল না। এমতাবস্থায় ফলটির মাংসল অংশের সহিত সমতা রাখিয়া উহার একাংশে ১ ইঞ্চি ভাজ পড়িবে। হয়তো উহার ২ ইঞ্চি উঁচু ও ২ ইঞ্চি নিচু হইয়া ভাজ পড়িবে। ভঁজের রকম ও সংখ্যা যতই হউক না কেন, উহাদের যোগফল হইবে ১ ইঞ্চি।
এককালে পৃথিবীর অবস্থাও ঐরূপই হইয়াছিল। তাপ ত্যাগ করিয়া ভূগর্ভস্থ তরল পদার্থ যে পরিমাণ সঙ্কুচিত হইল, বাহিরের ত্বকাংশ (কঠিন গ্রানাইট স্তর) সেই অনুপাতে সঙ্কুচিত হইতে না পারায় উহাতে ভঁজের সৃষ্টি হইল। ইহাতে ভূপৃষ্ঠের কোথায়ও উঁচু এবং কোথায়ও নিচু হইল ও কিছুটা সমতল থাকিল। বলা বাহুল্য যে, উঁচু স্থানগুলি পর্বত, নিচু স্থানগুলি সমুদ্রগহবর এবং অবশিষ্টভাগ সমতল ভূমি হইল।
ভূবিজ্ঞানীগণ বলেন যে, কোনো পর্বতই চিরকাল স্থায়ী থাকে না। পদার্থের ক্ষয় বা রূপান্তর অনিবার্য। তাপ, আলো ও বায়ুর প্রভাবে কঠিন প্রস্তর, এমনকি লৌহেরও রূপান্তর ঘটে। পর্বতের প্রস্তরাদি নিয়ত ক্ষয় হইয়া নানা উপায়ে উহা সমুদ্রে পতিত হয় ও সমুদ্রকে ভরাট করিতে থাকে। ইহার ফলে পর্বতের উচ্চতা এবং সমুদ্রের গভীরতা কমিয়া কালক্রমে ভূপৃষ্ঠ প্রায় সমতলে পরিণত হয়। পৃথিবীর ক্রমিক সঙ্কোচনের ফলে কালক্রমে আবার নূতন ভাজ পড়িতে আরম্ভ করে এবং পুনঃ পর্বত ও সাগরের সৃষ্টি হয়।
এক একবার পাহাড়াদির সৃষ্টি ও বিলয়কে বলা হয় এক একটি বিপ্লব। প্রতিটি বিপ্লবের ব্যাপ্তিকাল কোটি কোটি বৎসর। সৃষ্টির পর পৃথিবীতে এইভাবে পর্বতাদির সৃষ্টি ও বিলয় হইয়াছে দশবার। ইহার মধ্যে জীব সৃষ্টির পূর্বে ছয়বার এবং পরে চারিবার বিপ্লব ঘটিয়াছে। সর্বশেষ বিপ্লব অর্থাৎ বর্তমান বিপ্লবটি শুরু হইয়াছে প্রায় ৭ কোটি বৎসর আগে। তাই আধুনিক সাগর ও পাহাড়গুলির বয়স সাত কোটি বৎসরের কিছু কম। ভূবিজ্ঞানীগণ বলেন যে, বর্তমান বিপ্লবটি। এখনও শেষ হয় নাই অর্থাৎ পর্বতাদি এখনও বৃদ্ধি পাইতেছে। তবে উহা পাঁচ-দশ হাজার বৎসরে নজরে পড়ে না।
পৃথিবীর যাবতীয় সাগর ও পাহাড়ের পরিমাণ প্রায় সমান। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতের উচ্চতা প্রায় ৫ মাইল এবং গভীরতম সমুদ্রের গভীরতাও প্রায় ৫ মাইল।
হাল্কা-পরমাণুঘটিত পদার্থগুলি ভারি-পরমাণুঘটিত পদার্থের সহিত সমান তালে জমাট বাঁধিতে পারে না। ভূপৃষ্ঠে পর্বতাদি সৃষ্টির সময় পর্যন্ত হাইড্রোজেনাদি হাল্কা বায়বীয় পদার্থগুলি জমাট বাধিতে পারে নাই। অতঃপর পৃথিবীর তাপ আরও কমিলে বায়বীয় পদার্থ জমিতে আরম্ভ করে। ২টি হাইড্রোজেন ও ১টি অক্সিজেন পরমাণু যুক্ত হইয়া জলের অণুর সৃষ্টি হয় এবং কালক্রমে আকাশের তাপ আরও কমিলে জলের অণুগুলি সংযুক্ত হইয়া বৃষ্টির আকারে ভূপতিত। হয় এবং উহা নিচু গহ্বরগুলিতে আশ্রয় লইলে সাগরাদির সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর সমস্ত জলের আয়তন ১৫০ কোটি ঘনকিলোমিটার।
মৌলিক পদার্থগুলির অধিকাংশই বায়বীয় অবস্থা ত্যাগ করিয়া কঠিন ও তরল আকারে পৃথিবীতে আশ্রয় লইলে, অবশিষ্ট নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, আর্গন, নিয়ন, ক্রিপ্টন, হিলিয়াম, ওজন, জেনন ইত্যাদি বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়া সৃষ্টি হয় বাতাসের।
বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, পৃথিবীর বয়স প্রায় ৪০০ কোটি বৎসর। কোনোও মতে ৫০০ কোটি বৎসর। সৃষ্টির আদিতে পৃথিবীর আবর্তন (rotation) কাল ছিল ৪ ঘণ্টা এবং চন্দ্র ছিল মাত্র ৮ হাজার মাইল দূরে। উহা কালক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া বর্তমানে পৃথিবীর আবর্তনকাল হইয়াছে ২৪ ঘণ্টা এবং চন্দ্র গিয়াছে প্রায় ২৩৯ হাজার মাইল দূরে। পৃথিবীর আবর্তনকাল এবং চন্দ্রের দূরত্ব এখনও বাড়িতেছে। প্রতি একশত বৎসরে চন্দ্র ৫ ইঞ্চি দূরে সরিয়া যায় এবং ১২০ হাজার বৎসরে পৃথিবীর দিন এক সেকেণ্ড বাড়ে।[১৩]
বর্তমানে পৃথিবীর মেরুরেখা ২৩ ১/২ ডিগ্রী হেলিয়া আছে। কিন্তু ইহা চিরকাল একই রূপ থাকে।, বাড়ে ও কমে। এই বাড়া ও কমা একবার শেষ হইতে প্রায় ৪০ হাজার বৎসর সময় লাগে। এই মেরুরেখা পরিবর্তনের জন্য প্রতি ২৬ হাজার বৎসর পর পর পৃথিবীতে শীত ঋতুতে গ্রীষ্ম ঋতু এবং গ্রীষ্ম ঋতুতে শীত ঋতু আসে।
বর্তমানে পৃথিবীর কক্ষপথ ডিম্বাকার। কিন্তু ইহা চিরকাল একই আকৃতিতে থাকে না, কখনও গোল এবং কখনও ডিম্বাকার হয়। এইরূপ কক্ষপথের একবার আকার পরিবর্তনে সময় লাগে ৬০ হাজার হইতে ১২০ হাজার বৎসর।
বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, পৃথিবীর বর্তমান গড় উত্তাপ ৬৮° ফা.। কিন্তু ইহা চিরকাল একই মাত্রায় থাকে না, কোনো কোনো সময় অতিমাত্রায় কমিয়া যায়। এই সময়কে বলা হয় হিমযুগ। একলক্ষ বৎসরেরও কম সময় পর পর এক একটি হিমযুগ আসে। বর্তমান কালের হিমযুগটি গিয়াছে ৩০ হাজার বৎসর আগে এবং আগামী ৭০ হাজার বৎসরের মধ্যে আর একবার হিমযুগ আসিবে।[১৪]
হিমযুগের আগমনে পৃথিবীতে বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। হিমযুগে পৃথিবীর স্থলভাগের অধিকাংশ জায়গাই তুষারে ঢাকা পড়ে, তাই ঐ সব জায়গার উদ্ভিদাদি বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। বৃক্ষারোহী জন্তুরা সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিতে বাধ্য হয় এবং তুষারাবৃত জায়গার বাসিন্দারা কেহ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চলে চলিয়া যায়, কেহ গুহাবাসী হইয়া হিমকে গা-সহা করিয়া লয়; আর যাহারা উহার একটিও পারে না, তাহারা মারা পড়ে। যাহারা বাঁচিয়া থাকে, আবহাওয়া ও দেশ পরিবর্তনের ফলে তাহাদের আকৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্তন হইয়া অনেক নূতন জীবের উদ্ভব হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে খননকার্যের দ্বারা যে সকল জীবাশ্ম পাওয়া গিয়াছে, জীববিজ্ঞানীগণ তাহা পর্যবেক্ষণ পূর্বক জানিতে পারিয়াছেন যে, কোনো কোনো অঞ্চলে হিমযুগের পূর্ববর্তী বহু জন্তু লুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং হিমযুগের পূর্বে যে সব অঞ্চলে কোনো জীবের বসতি ছিল না, হিমযুগোত্তর কালে সেখানে কোনো কোনো জীবের বসবাস আরম্ভ হইয়াছে এবং অনেক অভিনব জীবের আবির্ভাব হইয়াছে। তাহারা আরও বলেন যে, বিগত হিমযুগে মানুষের বৃক্ষচারী পূর্বপুরুষগণ বৃক্ষশাখা ত্যাগ করিয়া গুহাবাস শুরু করিয়াছিল।
আর দুইটি মাত্র কথা বলিয়া এই আলোচনা শেষ করিব।
১. বিজ্ঞানের কতগুলি সিদ্ধান্ত আজগুবি ও অসম্ভব বলিয়া কাহারও মনে হইতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানের কোনো সিদ্ধান্তই আজগুবি নহে, প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তের পিছনে একাধিক প্রমাণ ও যুক্তি আছে। স্থানাভাবে এইখানে যুক্তি-প্রমাণের কোনোরূপ ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয় নাই। বিজ্ঞানের বিবিধ পুস্তকে উহার সবিস্তার বর্ণনা পাওয়া যাইতে পারে।
২. বিজ্ঞানে শেষ বলিয়া কিছু নাই। আজ যাহা সত্য বলিয়া গৃহীত হইল, ভবিষ্যতে তাহা মিথ্যা প্রমাণিত হইতে পারে এবং আজ যেখানে শেষ বলিয়া মনে হয়, তারপর আরও থাকিতে পারে; বিজ্ঞান এই সম্ভাবনাটিকে মানিয়া চলে। আর এইটিই বিজ্ঞানের বিশেষত্ব। অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী দূরবীক্ষণাদি যন্ত্র আবিষ্কারের সাথে সাথে বিশ্বের দৃষ্টিগোচর আকার ও আয়তন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। কাজেই অত্রপুস্তকের আলোচনাসমূহে যে সীমা ও সংখ্যা ব্যবহার করা হইল, ভবিষ্যতে তাহার পরিবর্তন অসম্ভব নহে।
————
১০. পৃথিবীর ঠিকানা, অমল দাসগুপ্ত, পৃ. ৫০।
১১. পৃথিবীর ঠিকানা, অমল দাসগুপ্ত, পৃ. ৬০,৬১।
১২ পৃথিবীর ঠিকানা, অমল দাসগুপ্ত, পৃ. ১৩৬।
১৩. পৃথিবীর ঠিকানা, অমল দাসগুপ্ত, পৃ. ৫, ৬, ২৮।
১৪. পৃথিবীর ঠিকানা, অমল দাসগুপ্ত, পৃ. ১৮১-১৮৪।
০৭. সূর্য
সূর্য
# পৌরাণিক মতবাদ
আনুষঙ্গিকভাবে সূর্য সম্বন্ধে এযাবত বিজ্ঞানসম্মত কিছু কিছু তথ্য আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু বিশেষভাবে উহা সম্বন্ধে কোনো আলোচনা করা হয় নাই। এখন সূর্য সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করা হইবে।
হিন্দুদের পুরাণে বর্ণিত আছে যে, কশ্যপ মুনির ঔরসে তৎপত্নী অদিতির গর্ভে সূর্যের জন্য হয়। সেইজন্য উহার আর এক নাম আদিত্য। ইনি রথে আরোহণ করিয়া আকাশ ভ্রমণ করেন এবং রথটিকে সাতটি ঘোড়া টানিয়া লয়। রথের সারথির নাম অরুণ।
পৌরাণিকেরা আরও বলেন যে, সূর্যদেব বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞাকে বিবাহ করেন। তাহার গর্ভে ইহার বৈবশ্বতমনু ও যম নামে দুই পুত্র এবং যমুনা নাম্নী এক কন্যা জন্মে। অতঃপর সংজ্ঞা স্বামীর তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া ছায়া নাম্নী এক রমণীর সৃজন করেন এবং তাহাকে স্বামীর নিকট রাখিয়া নিজে পলায়ন করেন। সূর্যের ঔরসে ছায়ার গর্ভে শনি নামে এক পুত্র ও তপতী নাম্নী এক কন্যা জন্মে। অতঃপর সূর্য প্রকৃত ঘটনা জানিতে পারিয়া সংজ্ঞার অন্বেষণে বাহির হন এবং উত্তর কুরুবর্ষে তাহাকে অশ্বিনীরূপে দেখিতে পান এবং সূর্য নিজেও অশ্বরূপ ধারণ করিয়া তাহার সহিত মিলিত হন (তিব্বতের উত্তর-পশ্চিমাংশ বা ইরান দেশকে অতিপূর্বকালে উত্তর কুরুবর্ষ বলা হইত)। সেই সময় হঁহার অশ্বিনীকুমার নামে দুই পুত্র জন্মে (ইহারা নাকি উভয়ে চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন)। অতঃপর বিশ্বকর্মা ঘঁহার তেজোহ্ৰাস করিয়া দিলে সংজ্ঞা পতিসহ সুখে বাস করিতে থাকেন। এতদ্ভিন্ন বানররাজ বালী ও সুগ্রীব এবং কুন্তির গর্ভজাত কর্ণও নাকি সূর্যের ঔরসজাত পুত্র।
শাস্ত্রোক্ত সূর্যদেবের স্ত্রী-পুত্ররা বোধ হয় যে, যমভিন্ন বুড়া হইয়া সকলেই মারা গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার নিজের আজও যৌবনকাল।
হিন্দু মতে, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মতো সূর্যও একজন দেবতা। লক্ষ্মী দেবী মানুষকে ধনরত্ন, সরস্বতী বিদ্যা-বুদ্ধি এবং সূর্যদেব তাপ ও আলো দান করিয়া থাকেন। লক্ষ্মী বা সরস্বতী দেবী কাহাকে কি পরিমাণ ধনরত্ন বা বিদ্যা-বুদ্ধি দান করিয়াছেন, কোনো ব্যক্তি তাহা পরিমাপ করিয়া দেখিতে পারে নাই। কিন্তু সূর্যদেব যে তাপ ও আলো দান করিতেছেন, তাহা পরিমাপ করা হইয়াছে; তবে তাহার উপকারিতা অপরিমেয়। তাই হিন্দুগণ অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা করেন। বৎসরে মাত্র একদিন, আর সূর্যদেবের পূজা করেন সংবৎসর, প্রতিদিন। এই পরমপূজ্য সূর্যদেবেরও সময় সময় একটি বিপদ আসে, তাহা হইল রাহুর গ্রাস বা গ্রহণ।
সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে হিন্দুদের পৌরাণিক আখ্যান এইরূপ — সমুদ্রমন্থনকালে রাহু ও কেতু নামক দৈত্যদ্বয় উপস্থিত না থাকায় উহারা সমুদ্রোখিত অমৃত-এর অংশ পায় নাই। যখন উহারা উপস্থিত হইল, তখন সমস্ত অমৃত দেবগণ বণ্টন করিয়া নিয়াছিলেন। অমৃতের অংশ না পাইয়া রাগান্ধ হইয়া কেতু চন্দ্রকে ও রাহু সূর্যকে গ্রাস করিয়া থাকে এবং কিয়ৎক্ষণ পরে আবার উদগীরণ করিয়া দেয়।
গ্রহণের সময় ইষ্টদেবের দুর্দশা দেখিয়া কিছুটা ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া হিন্দুগণ উঁহার বিপদ ও দুর্দশা মোচনের জন্য নানারূপ কোশেশ করিয়া থাকেন। আর্যরা হয়তো মনে করিতেন যে, রাহুর গ্রাসে পতিত হইয়া সূর্যদেব অতিশয় কষ্ট ভোগ করিতেছেন। অচিরে তাহাকে গ্রহণমুক্ত করিতে না পারিলে হয়তো তিনি মারাও যাইতে পারেন এবং তৎফলে বিশ্বজীবের বিশেষত মানব জাতির অমঙ্গল ঘটিতে পারে। তাই মানবকল্যাণ ও সূর্যদেবের আশুমুক্তির উদ্দেশ্যে আর্যরা করিয়াছেন হুলুধ্বনি, ঘণ্টা ও কাঁসর বাদন, গঙ্গাস্নান এবং কুম্ভমেলায় যাওয়ার ব্যবস্থা। আর তাহাদের এক সারিতে দাঁড়াইয়া মুসলমানগণ করিয়াছেন কসুফ ও খসুফ নামক নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা।
প্রাচীন মিশরীয়রা যখন নীলনদে নৌবিহার করিত, তখন আকাশের নীল রং দেখিয়া তাহারা ভাবিত –আকাশ যখন নীলবর্ণ, তখন উহাও হইবে একটি নদী বা সমুদ্র। কিন্তু ঐ নীল সাগরে সূর্যদেব চলে কি রকম? অত বড় সমুদ্র প্রত্যহ সঁতরাইয়া পার হওয়া সম্ভব নহে। বোধ হয় সূর্যদেব আমাদের মতোই রোজ রোজ নৌকায় ভ্রমণ করেন।
মুসলমানগণ বলিয়া থাকেন যে, সুর্যের বাহন নৌকা (বোধ হয় যে, ইহা প্রাচীন মিশরীয়দেরই অনুকরণ)। মুসলমানগণ আরও বলিয়া থাকেন যে, চতুর্থ আসমানে একখানা সোনার নৌকায় সূর্যকে রাখিয়া ৭০ হাজার ফেরেশতা সূর্যসহ নৌকাখানা টানিয়া পুর্ব হইতে পশ্চিম দিকে লইয়া যায়। সারারাত সুর্য আরশের নিচে বসিয়া
আল্লাহর এবাদত করে এবং প্রাতে পুনরায় পূর্ব দিকে হাজির হয়। এককালে মানুষের ধারণা ছিল যে, আকাশ একটি ছাদের মতো এবং চন্দ্র-সূর্য ও তারকারা তাহার গায়ে লটকানো আছে। তখন প্রশ্ন হইল, উহারা চলিতেছে কিভাবে? উত্তরে সেকালের পণ্ডিতগণ বলিলেন, আকাশ ঘোরে। আবার প্রশ্ন হইল, কেন ঘোরে? উত্তর হইল, বাতাসে। এই সম্বন্ধে আমাদের অঞ্চলে একটি পল্লীগীতি আছে। উহার ধূয়াটি এইরূপ —
হাওয়ার জোরে আসমান ঘোরে।
সঙ্গে লইয়া শেতারা,
গুরুর বাক্য শুনিয়া লও তোরা।
ইহার পর আবার প্রশ্ন উঠিল, আকাশ ঘুরিলে, চন্দ্র, সূর্য ও তারকারা একই গতিতে চলিত, উহারা ভিন্ন ভিন্ন গতিতে চলে কেন? ইহার উত্তর দিলেন ধর্মগুরুরা, বলিলেন –উহাদিগকে স্বর্গদূতেরা টানে।
পরবর্তীকালের যুক্তিবাদীরা সাব্যস্ত করিলেন যে, আকাশ ঘোরে বটে, তবে উহা সংখ্যায় একটি নহে, কয়েকটি। তাহারা দেখিলেন যে, চন্দ্র, সূর্য ও তারাদের চলিবার গতি ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং উহারা ভিন্ন ভিন্ন তিন আকাশে অবস্থিত। আবার তারাদের মধ্যে চারিটি বিশেষ তারা (গ্রহ) যথা–শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি– ইহাদের চলিবার গতি ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং উহারাও ভিন্ন ভিন্ন চারি। আকাশে অবস্থিত। কাজেই আকাশ সাতটি। বোধহয় যে, এইরূপ ধারণার ফলেই ‘সপ্ত আকাশ’ কথাটির উৎপত্তি হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, তখনকার লোকে বুধ বা অন্যান্য গ্রহদের বিষয়ে কিছুই জানিতেন না।
.
# আধুনিক মতবাদ
পুরানো ধারণা ও ধর্মীয় মতবাদের মূলে ছিল অলীক কল্পনা ও অন্ধবিশ্বাস। অন্ধবিশ্বাসের মূলে প্রথম আঘাত দিলেন পিথাগোরাস নামক একজন গণিতজ্ঞ প্রায় আড়াই হাজার বৎসর আগে। তিনি বলিলেন, সূর্য পৃথিবীকে আবর্তন করে না, সূর্যকে আবর্তন করে পৃথিবী। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে পুরানো ভ্রান্ত মতবাদের অপনোদন করিয়া বহুল খাঁটি সত্যের সন্ধান দেন রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কোপারনিকাস। ইহার একশত বৎসর পরে গ্যালিলিও দূরবীন আবিষ্কার করিয়া জ্যোতিষ্কলোকের জটিল রহস্যোদঘাটনের দ্বার খুলিয়া দেন। ধর্মীয় কোনো মতবাদের বিরুদ্ধে সত্যের সন্ধান করা ছিল তখন গুরুতর অপরাধ (কতকটা আজও)। কিন্তু সত্যের সন্ধানী গ্যালিলিও মানুষের জ্ঞানসমুদ্রে যে ঢেউ তুলিয়া গিয়াছেন, তাহা আজ বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে এবং সেই আঘাতে আজ অন্ধবিশ্বাসের বেলাভূমিতে গুরুতর ভাঙ্গন ধরিয়াছে।
আধুনিক সৌরবিজ্ঞানীগণ সূর্য সম্বন্ধে এত অধিক তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন যে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সেই সব আলোচনা করা অসম্ভব। এইখানে মাত্র গুটিকতক তথ্যের সারাংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল।
আকার আপাতদৃষ্টিতে সূর্যকে একখানা থালার মতো চ্যাপ্টা-গোল দেখা যায়। কিন্তু আসলে সূর্য থালাকৃতি নহে, ফুটবলের মতো গোল। তবে আয়তনে বৃহৎ এক অগ্নিপিণ্ড।
আয়তন আমাদের পৃথিবীর তুলনায় সূর্য আয়তনে প্রায় ১৩ লক্ষ গুণ বড়। সূর্যের ব্যাস প্রায় ৮ লক্ষ ৬৪ হাজার মাইল। ইহা পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ১০৮ গুণ। পৃথিবী হইতে সূর্য আয়তনে যত বড়, ওজনে তত বেশি নহে। ইহার কারণ এই যে, যে বাষ্পরাশি দ্বারা সূর্যের দেহ গঠিত, তাহার ওজন পৃথিবীর মাটির ওজনের ১ অংশ মাত্র। তথাপি সূর্যের ওজন প্রায় ২ x ১০২৭ টন। অর্থাৎ দুই-এর ডাহিনে সাতাশটি শূন্য।
আমাদের পৃথিবীর পরিধি প্রায় ২৫ হাজার মাইল। ঘণ্টায় ৫০ মাইল বেগবিশিষ্ট কোনো যানে আরোহণ করিয়া একবার ইহাকে প্রদক্ষিণ করিতে সময় লাগে প্রায় ২১ দিন। কিন্তু ঐরকম বেগবিশিষ্ট কোনো যানে আরোহণ করিয়া সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে চাহিলে সময় লাগিবার কথা প্রায় ৭ বৎসর। কিন্তু এত বড় বস্তুটিকেও দেখা যায় একখানা থালার মতো। ইহার কারণ এই যে, সূর্য বহুদূরে অবস্থিত।
দূরত্ব পৃথিবী হইতে সূর্যের মোটামুটি দূরত্ব ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। এই দূরত্বটি লিখিতে বা পড়িতে সময় লাগে দুই-এক সেকেণ্ড মাত্র। কিন্তু পূর্বোক্ত বেগবিশিষ্ট কোনো যানে আরোহণ করিয়া পৃথিবী হইতে সূর্যে পৌঁছিতে সময় লাগিবে প্রায় ২১৩ বৎসর। অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের সময় (১৭৫৭) পৃথিবী হইতে যাত্রা করিতে পারিলে সূর্যে পৌঁছান যাইত বাংলাদেশ স্বাধীন হইবার আগের বৎসর (১৯৭০)।
অবস্থা সাধারণভাবে সূর্যকে একটি উজ্জ্বল নিরেট পদার্থ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সূর্য একটি নিরেট পদার্থ নহে, উহার সমস্তটিই জ্বলন্ত বাম্প। সৌরবিজ্ঞানীগণ বলেন যে, সূর্যের আসল দেহটি সম্ভবত তরল বা ঘন বাষ্প দিয়া গড়া এবং উহা অনুজ্জ্বল। কিন্তু সাধারণত উহা আমাদের নজরে পড়ে না। আমাদের পৃথিবীকে ঘিরিয়া যেমন একটি বায়ুমণ্ডল আছে, সূর্যকে ঘিরিয়া সেইরূপ তিনটি বাষ্পীয় আবরণ আছে। যথা –আলোকমণ্ডল (Photosphere), বর্ণমণ্ডল (Chromosphere) ও ছটামণ্ডল (Corona)।
আলোকমণ্ডল পৃথিবীর নদী-সমুদ্ৰাদির জল যেমন বাষ্প হইয়া আকাশে উঠিয়া ঠাণ্ডা হইয়া মেঘে রূপান্তরিত হয়, সূর্যের আলোকমণ্ডল এইরকম মেঘের মতোই কিছু। তবে উহা পৃথিবীর মেঘের মতো ঠাণ্ডা ও অনুজ্জ্বল নহে। উহা সর্বদা জ্বলিয়া-পুড়িয়া প্রচণ্ড তাপ দেয়। সূর্য হইতে আমরা যে তাপ ও আলো পাইয়া থাকি, তাহা এই আলোকমণ্ডল হইতেই আসে। এই তাপ সম্বন্ধে কোনো একজন বিজ্ঞানী বলিয়াছেন যে, যদি সমস্ত সূর্যটিকে ৭০ ফুট গভীর বরফ দ্বারা মোড়া হয়, তবে সূর্যের তাপে তাহা এক মিনিটে গলিয়া যাইতে পারে। আর একজন বিজ্ঞানী বলিয়াছেন যে, সূর্যপৃষ্ঠের ৩ x ৩ ফুট জায়গা হইতে এক ঘণ্টায় যে পরিমাণ তাপ নির্গত হয়, পৃথিবীতে ঐ পরিমাণ তাপ উৎপন্ন করিতে হইলে কয়লা পোড়াইতে হইবে ১৭০ মণ।
উনুনের আগুনের তাপ সাধারণত গজখানেকের বেশি দূরে ছড়ায় না এবং শহর-বন্দরে যে সব বড় বড় অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়া থাকে, তাহার তাপও দুই-একশত গজের বেশি দূরে অনুভূত হয় না। জাপানের নাগাসাকি ও হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে যে অভূতপূর্ব উত্তাপের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার রেশও বাংলাদেশে আসিয়া পৌঁছে নাই। কিন্তু নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূর হইতে আসিয়া সূর্যোত্তাপ আমাদের অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, আলোকমণ্ডলের তাপ অর্থাৎ সূর্যের পৃষ্ঠের তাপের পরিমাপ ৬ হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড এবং কেন্দ্রপ্রদেশের তাপ ৪ কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।
কোনোরূপ তৈলাক্ত পদার্থ বা কাষ্ঠাদি জ্বালাইয়া আমরা অগ্নি উৎপাদনপূর্বক তাহার আলো ব্যবহার করিয়া থাকি এবং বিজ্ঞানীগণ বৈদ্যুতিক আলো, গ্যাসবাতির আলো ইত্যাদি অনেক রকম আলো উৎপন্ন করেন। কিন্তু সূর্যালোকের সমকক্ষ আলো আজ পর্যন্ত কেহই সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলেন যে, সূর্যের আলো ছয় লক্ষ পূর্ণচন্দ্রের আলোকের সমান।
সৌরকলঙ্ক— চন্দ্রের কলকের ন্যায় সূর্যেরও কলঙ্ক আছে। এ সম্বন্ধে জ্যোতির্বিদগণ বলেন যে, সূর্যের আলোকমণ্ডলে সর্বদা আগুনের ঝড় হয় এবং সেই ঝড়ের তাণ্ডবে আলোকমণ্ডলের কোনো কোনো স্থান ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সেই বিচ্ছিন্ন স্থান বা ফাঁক দিয়া সময়ে সময়ে সূর্যের অনুজ্জ্বল আসল দেহ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাই সূর্যের কলক। চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় সূর্যের কোনো কলক চিরস্থায়ী নহে। সূর্যপৃষ্ঠে কোথাও কোনো কলঙ্ক দেখা দিলে উহা কয়েক দিন বা কয়েক মাস থাকিয়া মিলাইয়া যায়, আবার কোথায়ও নূতন কলঙ্ক দেখা দেয়। এগারো বৎসর পর পর সৌরকলক বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কিন্তু কেন যে এগারো বৎসরে একবার সৌরকলঙ্ক বাড়ে, তাহা এখনও অজ্ঞাত।
স্বাভাবিক অবস্থায় সূর্যের আলোকমণ্ডল হইতে যে পরিমাণ তাপ ও আলো বিকীর্ণ হইয়া থাকে, সৌরকলঙ্ক বৃদ্ধি পাইলে তখন আর সেই পরিমাণ তাপ ও আলো বিকীর্ণ হইতে পারে না, কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। শোনা যায় যে, কোনো একজন বিজ্ঞানী একটি গাছের গুঁড়ি পর্যবেক্ষণ করিবার সময়ে দেখিলেন যে, খুঁড়িটির কেন্দ্র হইতে স্তরে স্তরে তাহার আয়তন বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্তরগুলি সম্ভবত খুঁড়িটির বার্ষিক বৃদ্ধির চিহ্ন। তিনি আরও দেখিলেন যে, প্রতি এগারোটি স্তরের পর এমন একটি বিশেষ স্তর দৃষ্ট হয়, যাহা অন্য সকল স্তর হইতে ভিন্ন ধরণের। তিনি জানিতেন যে, প্রতি এগারো বৎসর পর পর সৌরকলঙ্ক বাড়ে। তাই তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, সেই গুঁড়িটির ঐ বিশেষ স্তরগুলি হয়তো সৌরকলঙ্কেরই প্রতিক্রিয়ার ফল। সৌরকলঙ্ক পৃথিবীর আবহাওয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।
বিজ্ঞানীগণ দেখিয়াছেন যে, যে সকল কলঙ্ক মাসাধিককাল স্থায়ী হইয়া থাকে, উহারা সূর্যের এক প্রান্ত হইতে উদিত হইয়া অপর প্রান্তে অস্ত যায়। তাহারা আরও লক্ষ্য করিয়াছেন যে, কোনো একটি বিশেষ কলক একবার সূর্যকে আবর্তন করিয়া ২৭ দিনে পুনঃ স্বস্থানে ফিরিয়া আসে। তাই তাঁহারা বলেন যে, পৃথিবীর আহ্নিক গতির ন্যায় সূর্যেরও একটি গতি আছে। নিজ মেরুদণ্ডের উপর একবার আবর্তিত হইতে যেমন পৃথিবীর সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা, তেমন সূর্যের লাগে ২৭ দিন। আপাতদৃষ্টিতে স্থির দেখা গেলেও আসলে সূর্য আবর্তনশীল।
বর্ণমণ্ডল ও ছটামণ্ডল আমরা সূর্যের যে চেহারা দেখিতে পাই, তাহা হইল তাহার আসল দেহের উপর আলোকমণ্ডলের আচ্ছাদন। ইহার উপর তাহার আরও দুইটি আবরণ আছে। কিন্তু আলোকমণ্ডলের প্রচণ্ডতায় তাহা আমাদের নজরে পড়ে না। সূর্যগ্রহণের সময়ে যখন আলোকমণ্ডল ঢাকা পড়ে, তখন অল্প সময়ের জন্য বর্ণমণ্ডল ও ছটামণ্ডলকে দূরবীক্ষণ দ্বারা স্পষ্ট দেখা যায়। বর্ণমণ্ডলের গভীরতা ৩–১০ হাজার মাইল। দাউদাউ করিয়া সেখানে আগুন জ্বলে। সময়ে সময়ে তাহার কোনো কোনো শিখা সূর্যের আকাশে ৫০ হাজার মাইল পর্যন্ত উর্ধে উঠিয়া থাকে। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে যে সূর্যগ্রহণটি হইয়াছিল, তখন বিজ্ঞানীগণ একটি শিখাকে প্রায় আড়াই লক্ষ মাইল উঁচু হইতে দেখিয়াছিলেন। বাস্তবিকই সূর্যের দেহটি আগুন দিয়া গড়া এবং সেখানে নিয়ত চলিতেছে আগুনের প্রবল বন্যা।
বর্ণমণ্ডলের পরে আছে ছটামণ্ডল। এইখানেও নানাবিধ বাষ্প জ্বলিয়া থাকে। তবে ইহার তাপ অপেক্ষাকৃত মৃদু। অন্য দুই মণ্ডলের ন্যায় এই মণ্ডলের গভীরতা পাঁচ-দশ হাজার মাইল নহে, লক্ষ লক্ষ মাইল ইহার গভীরতা। ১৮৭৮ সালে বিজ্ঞানীরা সূর্যগ্রহণের সময়ে সূর্যের এক কোটি মাইল দূরে ছটামণ্ডল দেখিয়াছিলেন।
.
# উপকারিতা
বিজ্ঞানীদের মতে, সৌররাজ্যের বস্তুসমূহের বৃহত্তম গ্রহ-উপগ্রহ হইতে ক্ষুদ্রতম অণু-পরমাণু পর্যন্ত, সবই সূর্য হইতে উদ্ভূত, এমনকি প্রাণও। সৌরশক্তির প্রভাবে আবহাওয়ার বিবর্তনের ফলে এককালে পৃথিবীতে এমন একটি অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল, যখন সাগরজলে সৃষ্টি হইয়াছিল কলয়ডাল সলিউশন নামক আদিম জৈব পদার্থের। সেই জৈব পদার্থটি হইতে ধাপে ধাপে নানাবিধ জীবের উৎপত্তি হইয়াছে এবং কিভাবে হইয়াছে, তাহার কিছু আলোচনা করা হইবে পরবর্তী এক পরিচ্ছেদে। কিন্তু শুধু জীবন উৎপত্তির জন্যই নহে, জীবনের রক্ষার জন্যও সৌরশক্তি অপরিহার্য।
প্রত্যক্ষভাবে সূর্য আমাদের দুইটি বস্তু দান করিয়া থাকে –তাপ ও আলো। এই আলোই জীবের চক্ষু দান করিয়াছে, আবার সেই চক্ষু আলোর মাধ্যমে জগত প্রত্যক্ষ করিতেছে। এই বিষয়টি বোধ হয় আর একটু বাড়াইয়া বলা আবশ্যক। অ্যামিবা বা স্পঞ্জের মতো ইন্দ্রিয়বিহীন জীবের পর্যায় পার হইয়া যে সকল জীব আলোর সংস্পর্শে বাস করিতেছিল, তাহাদের দেহের এক শ্রেণীর কোষ (cell) আলোক গ্রহণে উন্মুখ হয় এবং লক্ষ লক্ষ বৎসর সমবেত চেষ্টার ফলে দুর্শনেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। পক্ষান্তরে যাহারা আলোর সংস্পর্শলাভে বঞ্চিত হইয়াছিল, তাহারা হয় চক্ষুহীন বা অন্ধ। যেমন কেঁচো, উইপোকা ইত্যাদি। এই দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা আলোর মাধ্যমে জীব বিশেষত মানুষ উপভোগ করিতেছে জগতের যত সব রূপমাধুরী। হীরকের ঔজ্জ্বল্য, স্বর্ণের চাকচিক্য, পুষ্পের সৌন্দর্য ও রমণীর কান্তি –আলোকের অভাবে সমস্তই মিশিয়া যাইত এক অব্যক্ত অন্ধকারে। পক্ষান্তরে সে অন্ধকার উপভোগ করিবার মতো একটি প্রাণীও থাকিত না পৃথিবীতে, যদি সূর্য তাপ বিতরণ না করিত।
সূর্যের তাপে সমুদ্ৰাদির জল বাষ্পে পরিণত হইয়া আকাশে উঠিয়া মেঘ হয় এবং সূর্যের তাপে বায়ু গতিশীল হয়। তাই বায়ুপ্রবাহের দ্বারা জলভাগের উপরিস্থিত মেঘরাশি স্থলভাগে নীত হয় এবং বৃষ্টিপাত হয়। সেই বৃষ্টিপাতের ফলে ভূপৃষ্ঠে নানারূপ তরু-তৃণ জন্মায় এবং সূর্যালোকপ্রাপ্তির ফলে বৃক্ষপত্রে ক্লোরোফিল জন্মিয়া উদ্ভিদের খোরাকি জোগায় ও দেহ পুষ্ট করে (পরবর্তীতে ক্লোরোফিল সম্বন্ধেও আলোচনা করা হইবে)। নিরামিষভোজী জীবেরা সেই তরুরাজির পাতা-পল্লব ও ফলমূলাদি ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে এবং আমিষভোজী জীবেরা নিরামিষভোজীদের মাংস ভক্ষণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। মূলত পৃথিবীকে সজীব করিয়া রাখিয়াছে একমাত্র সূর্য।
.
# শক্তি
সূর্য নিয়ন্ত্রণ করে গ্রহজগতের বিশেষত পৃথিবীর সব কিছু –প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে, মুখ্য বা গৌণভাবে। বলা যায় যে, সৌরজগতের পার্থিব বা অপার্থিব যাবতীয় শক্তির উৎসই হইল সূর্য। শক্তি বিকাশের কয়েকটি বিশেষ রূপ আছে। যেমন –তাপশক্তি, আলোকশক্তি, বিদ্যুৎশক্তি, মহাকর্ষশক্তি ইত্যাদি। এইখানে সূর্যের মহাকর্ষশক্তি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতেছে।
মহাকর্ষের নিয়ম মাফিক জগতের প্রতিটি বস্তু একে অন্যকে আকর্ষণ করে। আকর্ষণী শক্তির ন্যূনাধিক্য নির্ভর করে বস্তুদ্বয়ের ওজন ও দূরত্বের উপর। যে বস্তুর ওজন যত বেশি, তাহার আকর্ষণী শক্তি তত অধিক। পক্ষান্তরে বস্তুদ্বয়ের দূরত্ব বৃদ্ধি পাইলে আকর্ষণী শক্তি কমিয়া যায়। ভূপৃষ্ঠের যাবতীয় বস্তুর চেয়ে পৃথিবী ওজনে ভারি। তাই ভূপৃষ্ঠের সকল বস্তুকে সে নিজের কোলের দিকে টানিয়া রাখিতেছে, এমনকি বাতাসকেও। তাই সম্ভব হইয়াছে ভূপৃষ্ঠে জীবাদি বস্তুসমূহের স্থিতি। পৃথিবী যদি টানিয়া না রাখিত, তবে বায়ুসমেত মানুষ, পশু-পাখি ও বৃক্ষাদি নিমেষে মহাশূন্যে উড়িয়া যাইত, এমনকি বালুকণাও। আর যদি বায়ু থাকিত আকর্ষণমুক্ত, তবে পৃথিবীর আহ্নিকগতির ফলে ভূপৃষ্ঠে প্রতি ঘণ্টায় ১,০৪১২ মাইল বেগে পশ্চিম দিকগামী ঝড় বহিত। কেননা পৃথিবীর আহ্নিকগতি বা আবর্তনের ফলে ভূপৃষ্ঠ উক্ত বেগে পূর্বদিকে সরিয়া যাইতেছে। সেই প্রলয়ঙকরী ঝড়ের মুখে ভূপৃষ্ঠে টিকিয়া থাকিত না কোনো পর্বতও। বস্তুত পৃথিবীর সমস্ত সৌরভ-গৌরবের মূলে নিহিত রহিয়াছে তাহার মহাকর্ষশক্তি। অনুরূপভাবে সূর্য স্বীয় আকর্ষণে বাঁধিয়া তাহার চতুর্দিকে পৃথিবীকে ঘুরাইতেছে। আর তাহারই ফলে হইতেছে দিন রাত্রি, ঋতু-বৎসর এবং বজায় থাকিতেছে পৃথিবীতে জীববাসের অনুকূল আবহাওয়া। যদি সূর্যের আকর্ষণ না থাকিত, তবে পৃথিবী ছুটিয়া চলিত অনির্দিষ্ট মহাশূন্যে। সেখানে পৃথিবী হইত অন্ধকার শৈত্যরাজ্যে জনপ্রাণীহীন একটি বস্তুপিণ্ড।
বলিতে শুরু করিয়াছিলাম সূর্যের আকর্ষণশক্তির কথা। কোনো ব্যক্তি এক পোয়া বা এক সের ওজনের কোনো একটি পদার্থে রশি বাঁধিয়া নিজের চারিপার্শ্বে উহাকে চক্রাকারে ঘুরাইতে পারে, কিন্তু সেই ব্যক্তি নিজের বা তাহার চেয়ে বেশি ওজনের কোনো পদার্থকে ঐরূপ ঘুরাইতে পারিবে না, ঘুরাইতে চাহিলে সে নিজেই স্থানচ্যুত হইবে। সূর্য একস্থানে দাঁড়াইয়া তাহার আকর্ষণের রশিতে বাধিয়া গোটা এগারো গ্রহকে প্রতিনিয়ত ঘুরাইতেছে। ইহা সহজ ব্যাপার নহে। কোলের কাছে যে বুধ গ্রহটি আছে, তাহাকে ঘুরানো সহজ হইলেও প্রায় ২৮০ কোটি মাইল দূরে অবস্থিত ১৭টি পৃথিবীর সমান ওজনের নেপচুন গ্রহটিকে ঘুরাইতে যে কতটুকু শক্তির দরকার, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়। সূর্যের শক্তি কম্পনার অতীত। কিন্তু সূর্যগ্রহণের ব্যাখ্যাকম্পে পৌরাণিকগণ এত অধিক শক্তিশালী সূর্যটিরও রাহুর হস্তে পরাজয় ঘটাইয়াছেন। বস্তুত সূর্যগ্রহণের আধুনিক তথ্য নিম্নরূপ।
আকাশ বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, সূর্যকে কেন্দ্র করিয়া প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে থাকিয়া ৩৬৫ দিন ৬ ১/৪ ঘণ্টায় পৃথিবী একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে এবং পৃথিবীকে কেন্দ্রে রাখিয়া প্রায় ২ লক্ষ ৩৯ হাজার মাইল দূরে থাকিয়া প্রায় ২৯ ১/২ দিনে চন্দ্র একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই ঘোরাফেরায় কোনো কোনো সময়ে চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী এক সরলরেখায় দাঁড়ায়। সেই সময়ে পূর্ণিমা তিথি হইলে চন্দ্র ও সূর্যের মাঝখানে পৃথিবী অবস্থান করার ফলে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রে পতিত হইয়া চন্দ্রকে ঢাকিয়া ফেলে, আমরা উহাকে চন্দ্রগ্রহণ বলি এবং ঐ সময়ে অমাবস্যা তিথি হইলে পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে চন্দ্র দাঁড়াইয়া সূর্যকে ঢাকিয়া রাখে, আমরা উহাকে সূর্যগ্রহণ বলি। আসলে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হইল পৃথিবী ও চন্দ্রের ছায়ামাত্র; রাহু, কেতু বা অন্য কিছু নহে।
.
# মৃত্যু
পৌরাণিকগণ বলেন –ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কার্তিক, গণেশ, ইন্দ্র, চন্দ্র, সূর্য এবং লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, দুর্গা ইত্যাদি দেব-দেবীগণ সকলেই অমৃত পান করিয়া অমর হইয়াছিলেন। কিন্তু চন্দ্র ও সূর্যদেব ছাড়া বিশ্বের কোথায়ও উহাদের অন্য কাহারও কোনো খোঁজ-খবর মিলিতেছে না। সম্ভবত উহাদের সকলেরই তিরোধান ঘটিয়াছে। তবে কি চন্দ্র ও সূর্যদেব বাস্তবিকই অমর?
আকাশ বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, চন্দ্রদেবের মৃত্যু ঘটিয়াছে লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্বে। আমরা এখন দেখিতেছি মৃত চন্দ্রের ককাল। চন্দ্রদেবের গায়ে এখন তাপ নাই, রক্ত (জল) নাই; অধিকন্তু তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস (বায়ু) নাই। আর জল, বায়ু ও তাপ নাই বলিয়া চন্দ্রদেবের মরদেহে একটি কীটও (প্রাণী) নাই। চন্দ্রদেব এখন বাস্তবিকই নির্জীব। সূর্যদেবের মৃত্যু সম্বন্ধে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা রহিয়াছে ‘প্রলয়’ পরিচ্ছেদে।
০৮. গ্রহমণ্ডলী
গ্রহমণ্ডলী
ধর্মীয় মতে, বিশ্বে বিশালতায় মাতা বসুন্ধরার সমকক্ষ আর কেহ নাই এবং তাহাররকোনো দোসর নাই। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে, বিশাল বিশ্বে আমাদের বসুমাতা একটি বালুকণা সদৃশও নহেন এবং বসুমাতা তাঁহার পিতার একমাত্র কন্যাও নহেন। হঁহারা সহোদর ভাই-ভগিনীতে বর্তমানে এগারো জন, অর্থাৎ এগারো গ্রহ।
বহুদিন পূর্ব হইতেই মানুষ কয়েকটি গ্রহের সন্ধান জানিত। তাহারা নক্ষত্র হইতে গ্রহদের পার্থক্য করিত শুধু উহাদের আলোতে ও গতিতে। তাহারা দেখিত যে, নক্ষত্রদের আলো মিটমিট করে আর গ্রহদের আলো স্থির এবং নক্ষত্ররা আকাশের বিশেষ স্থানে স্থায়ীভাবে বাস করে, কিন্তু গ্রহরা চলাফেরা করে। ইহা ভিন্ন গ্রহদের সম্বন্ধে তাহাদের আর বেশি কিছু জানা ছিল না।
বিজ্ঞানী জিনস ও জেফরিজ-এর মতে –প্রায় তিন শত কোটি বৎসর আগে (কোনো কোনো মতে পাঁচ শত কোটি বৎসর) কোনো একটি নক্ষত্র সূর্যের খুব নিকট দিয়া চলিয়া যাওয়ায় তাহার আকর্ষণে (কোনো মতে কেন্দ্ৰাপসারণী শক্তির প্রভাবে) সূর্যের দেহের খানিকটা অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং তাহা হইতে পৃথিবীসহ এগারোটি গ্রহের সৃষ্টি হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, সূর্য একটি অগ্নিপিণ্ড, উহার কেন্দ্রীয় অঞ্চলের তাপমাত্রা চারি কোটি ডিগ্রী সে. এবং বাহিরের অংশের তাপমাত্রা ছয় হাজার ডিগ্রী সে.। তাই গ্রহগণের জন্ম হইবার সময়ে তাহাদের কাহারও দেহের তাপ ছয় হাজার ডিগ্রীর কম ছিল না। আয়তন ও সূর্য হইতে দূরত্বের তারতম্যানুসারে দেহের তাপ ত্যাগ করিয়া কালক্রমে গ্রহরা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পৌঁছিয়াছে। সে যাহা হউক, আকাশ বিজ্ঞানীগণ গ্রহদের বর্তমান অবস্থার যে বিবরণ দিতেছেন, তাহার কিছু আলোচনা করিতেছি।
সচরাচর দেখা যায় যে, একই পিতার ঔরসজাত সন্তানদের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিগত কিছু না কিছু সাদৃশ্য থাকেই। বিজ্ঞানীদের মতে, গ্রহরা একই পিতার ঔরসজাত সন্তান। তাই যদি হইয়া থাকে, তবে উহাদের আকৃতি ও প্রকৃতিতে কিছু না কিছু সাদৃশ্য থাকা উচিত। এখন দেখা যাক যে, উহা কতদূর আছে।
.
# ১. বুধ
গ্রহ মাত্রই গোলাকার। কিন্তু সম্পূর্ণ গোল কেহই নহে। প্রত্যেক গ্রহেরই মেরুপ্রদেশ চাপা এবং এক গোলাকার কক্ষপথে নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু কোনো গ্রহের ঐ পথটি সম্পূর্ণ গোল নহে, দুইদিকে কিঞ্চিৎ চাপা, অর্থাৎ ডিম্বাকার; সূর্য আছে উহার কেন্দ্রবিন্দু হইতে একদিকে সামান্য সরিয়া। ইহাতে গ্রহগণ চলিবার সময়ে সূর্য হইতে উহাদের দূরত্ব সমান থাকে না, বাড়ে ও কমে। বুধ সূর্যের নিকটতম গ্রহ। সূর্য হইতে বুধ গ্রহের মোটামুটি দূরত্ব ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল। কিন্তু এই দূরত্ব বৃদ্ধি পাইয়া কোনো সময়ে হয় ৪ কোটি ৩৫ লক্ষ মাইল, আবার কমিয়া হয় ২ কোটি ৮৫ লক্ষ মাইল।
বুধ গ্রহের ব্যাস ৩,০০৮ মাইল। ইহা পৃথিবীর ব্যাসের অর্ধেকেরও কম। আয়তনে বুধ পৃথিবীর তুলনায় ০.০৬; অর্থাৎ প্রায় ১৭টি বুধ একত্র করিলে তবে পৃথিবীর সমান হইতে পারে। আয়তনে বুধ সকল গ্রহের মধ্যে ছোট, এমনকি বৃহস্পতির দুইটি চাঁদের চেয়েও ছোট। বুধ গ্রহের আহ্নিক। গতি অতি ধীর, দিন ও বৎসর সমান। উহার এক অংশে চিরকাল দিন ও অপর অংশে চিরকাল রাত্রি। আমাদের চন্দ্র যেমন তাহার এক অংশ পৃথিবীর দিকে রাখিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, বুধও তেমনি তাহার এক অংশ সূর্যের দিকে রাখিয়া গড়ে প্রতি সেকেণ্ডে ২৯.৭ মাইল বেগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। এই বেগ সব সময়ে সমান থাকে না। বুধ যখন সূর্যের কাছে থাকে, তখন তাহার চক্রবেগ হয় প্রতি সেকেণ্ডে ৩৬ মাইল এবং যখন দূরে থাকে, তখন হয় ২৪ মাইল। এইভাবে চলিয়া সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে বুধের সময় লাগে পৃথিবীর হিসাবে ৮৮ দিন।
যে গ্রহ সূর্যের যত নিকটে, তাহার কক্ষভ্রমণের গতিবেগ তত বেশি এবং যে গ্রহ যত দূরে, তাহার গতিবেগ তত কম। যেমন সূর্য হইতে বুধের দূরত্ব ৩ কোটি ৬০ লক্ষ মাইল এবং তাহার কক্ষভ্রমণের গতিবেগ সেকেণ্ডে প্রায় ৩০ মাইল। আর প্লুটোর দূরত্ব ৩৬৭ কোটি মাইল এবং তাহার কক্ষভ্রমণের গতিবেগৃ সেকেণ্ডে প্রায় ৩ মাইল মাত্র।
বুধ গ্রহ খুব ছোট বলিয়া তাহার কোনো উপগ্রহ নাই। বুধ সূর্যের খুব নিকটের গ্রহ বলিয়া উহার তাপমাত্রা অত্যধিক, এমনকি ফুটন্ত জলের চেয়েও বেশি। বুধের দেহ যে, সকল মাল মশলায় তৈয়ারী, তাহার গড় ওজন অর্থাৎ বস্তুগুরুত্ব (জলের অনুপাতে) ৩.৭৩। পৃথিবীর চেয়ে বুধ হাল্কা পদার্থের তৈয়ারী। স্মরণ রাখা দরকার যে, পৃথিবীর বস্তুগুরুত্ব ৫.৫২।
বিশ্বের যে কোনো পদার্থ অপর কোনো পদার্থকে তাহার নিজের কেন্দ্রের দিকে টানে। এই টানকে বলা হয় মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। যে পদার্থের ভর যত বেশি, তাহার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তত বেশি। ঐ শক্তির বলেই পৃথিবী আমাদিগকে টানিয়া রাখিতেছে। উপর দিকে বন্দুক বা কামান হুঁড়িলে তাহার গুলি বা গোলা যতই উপরে উঠুক না কেন, পৃথিবী তাহাকে টানিয়া ভূপাতিত করেই। যেহেতু কোনো গুলি বা গোলার বেগ সাধারণত সেকেণ্ডে ২-৩ মাইলের বেশি নহে, তাই উহারা পৃথিবীর আকর্ষণকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে না। কিন্তু কোনো গোলা বা গুলি বেগ যদি প্রতি সেকেণ্ডে ৭ মাইল হয়, তবে উহাকে পৃথিবী টানিয়া ফিরাইতে পারে না। তখন উহা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের সীমা ছাড়াইয়া মহাকাশে চলিয়া যায়। এই রকম বেগকে বলা হয় নিষ্ক্রমণ বেগ। বুধের নিষ্ক্রমণ বেগ মাত্র ২.৪ মাইল।
সাধারণত দেখা যায় যে, কোনো পদার্থ উত্তপ্ত হইলে তাহা আয়তনে বাড়ে। উহার কারণ এই যে, উত্তপ্ত পদার্থের অণুগুলির চঞ্চলতা বাড়ে। অর্থাৎ অণুগুলির কম্পনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং পরস্পর ধাক্কাধাক্কির ফলে অণুগুলি দূরে দূরে সরিয়া যায়, ইহাতে মূল বস্তুটি আয়তনে বাড়ে। কোনো বায়বীয় পদার্থ উত্তপ্ত হইয়া উহার অণুর গতিবেগ যদি ঐ গ্রহের নিষ্ক্রমণ বেগের সমান হয়, তবে ঐ বায়বীয় পদার্থকে সেই গ্রহ টানিয়া রাখিতে পারে না। উহা মহাকাশে উধাও হইয়া যায়।
বুধ গ্রহের নিষ্ক্রমণ বেগ মাত্র ২.৪ মাইল। অত্যধিক তাপপ্রযুক্ত বুধের জল ও বায়ুর অণুগুলির গতিবেগ বুধ গ্রহের নিষ্ক্রমণ বেগের সমান বা তাহারও বেশি হইয়াছিল বলিয়া উহারা সমুদয়ই মহাকাশে উড়িয়া গিয়াছে। বুধ গ্রহে জল ও বায়ুর কোনো অস্তিত্ব নাই। কাজেই সেখানে কোনো জীব বা জীবনের অস্তিত্ব নাই।
পৃথিবীর ভ্রমণপথের ভিতরে বুধের ভ্রমণপথ। তাই মাত্র কয়েক দিনের জন্য বুধকে দেখা যায়। পশ্চিম আকাশে সূর্যাস্তের পরে এবং মাত্র কয়েক দিন পূর্বের আকাশে সূর্যোদয়ের পূর্বে। তাহাও খালি চোখে নহে, দূরবীন যোগে।
বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, বুধ ঠিক ঔরসজাত না হইলেও সূর্যের পুত্রস্থানীয়। কেননা সূর্যের দেহ হইতেই বুধ জন্মলাভ করিয়াছে। কিন্তু হিন্দুদের পুরাণে বলে অন্য কথা। পুরাণে বলে — চন্দ্রের ঔরসে ও তারার গর্ভে বুধের জন্ম হয় এবং বুধ ইলা নাম্নী এক রমণীকে বিবাহ করে। এই ঘরে বুধের এক পুত্রও জন্মে, তাহার নাম পুরুরবা। বুধ নাকি চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ। বেশ মনোজ্ঞ কাহিনী। মৃত কি জীবিত যেভাবেই থাকুক, বুধ এখনও আকাশে আছে। কিন্তু তাহার স্ত্রী-পুত্র কোথায় গেল, তাহার কোনো হদিস নাই।
.
# ২. শুক্র
বুধের ভ্রমণপথের বাহিরে শুক্রের ভ্রমণপথ। সুতরাং শুক্র বুধের প্রতিবেশী এবং পৃথিবীরও। সূর্য হইতে শুক্রের দূরত্ব বুধের দূরত্বের প্রায় দ্বিগুণ। অর্থাৎ মোটামুটি ৬ কোটি ৭০ লক্ষ মাইল। কক্ষপথের বক্রতার দরুন এই দূরত্ব বৃদ্ধি পাইয়া কোনো সময়ে হয় ৬ কোটি ৭৫ লক্ষ মাইল, আবার কমিয়া হয় ৬ কোটি ৬৫ লক্ষ মাইল।
শুক্রের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের চেয়ে সামান্য কম। পৃথিবীর বিষুব অঞ্চলের ব্যাস ৭,৯২৬ মাইল, কিন্তু শুক্রের ৭,৫৭৬ মাইল। অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের চেয়ে ৩৫০ মাইল কম। আয়তনে শুক্র পৃথিকর আয়তনের প্রায় দশ ভাগের নয় ভাগের সমান। শুক্রের দেহ সব সময়ে গাঢ় ধূলির মেঘে আবৃত থাকায় উহার আহ্নিক গতি আছে কি না, তাহা এখনও জানা যায় নাই।
প্রতি সেকেণ্ডে ২১.৭ মাইল, অর্থাৎ প্রায় পৌনে বাইশ মাইল পথ চলিয়া প্রায় সাড়ে সাত মাসে শুক্র একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। সুতরাং আমাদের সাড়ে সাত মাসের সমান শুক্রের এক বৎসর। শুক্র গ্রহকে সঁঝের তারা বা পোয়াতে তারাও বলা হয়। কিন্তু প্রচলিত নাম শুকতারা। শুকতারাকে সকল সময়ে দেখা যায় না। শুকতারার ভ্রমণপথ পৃথিবীর ভ্রমণপথের ভিতরে অবস্থিত। তাই সূর্য প্রদক্ষিণের সময়ে দেখা যায় যেন শুকতারা কখনও সূর্যের আগে আগে চলে এবং কখনও চলে পিছনে। যখন আগে আগে চলে, তখন প্রায় সাড়ে তিন মাস উহাকে দেখা যায় পূর্ব আকাশে সূর্য উদয়ের পূর্বে এবং যখন পিছনে চলে, তখন দেখা যায় পশ্চিম আকাশে সূর্য অস্তের পরে। শুক্র পূর্ব আকাশে থাকিলে তখন তাহার নাম হয় পোয়াতে তারা এবং পশ্চিম আকাশে থাকিলে বলা হয় সাঁঝের তারা।
রাত্রের আকাশে শুক্রের মতো উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক দ্বিতীয়টি নাই। কিন্তু উহার উজ্জ্বলতা সব সময়ে সমান থাকে না। তাহার কারণ এই যে, পৃথিবীর ভ্রমণপথের ভিতরে শুক্রের ভ্রমণপথ থাকায় চন্দ্রকলার ন্যায় শুক্রকলারও হ্রাস-বৃদ্ধি এবং অমাবস্যা বা পূর্ণিমা হয়। তবে অমাবস্যা বা পূর্ণিমা ও তাহার কাছাকাছি সময়ে উহাকে দেখাই যায় না। যেহেতু ঐ সময়ে শুক্র সূর্যের প্রায় সাথে সাথেই উদিত হয় ও অস্ত যায়। কাজেই ঐ দুই সময়ে শুক্র থাকে সূর্যের আলোকসমুদ্রে ডুবিয়া। আর একটি কথা এইখানে জানিয়া রাখা ভালো যে, কেহ যদি বৃহস্পতি, শনি ইত্যাদি পৃথিবীর ভ্রমণপথের বাহিরে অবস্থিত কোনো গ্রহে বসিয়া পৃথিবীর গতিবিধি লক্ষ্য করিতে থাকেন, তবে তিনি পৃথিবীকে শুকতারার মতোই দেখিবেন এবং দেখিবেন চন্দ্রকলার মতোই তাহার কলার হ্রাস বৃদ্ধি, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা। তবে সময়ের ব্যবধান হইবে। আমাদের চন্দ্রের অমাবস্যা ও পূর্ণিমার ব্যবধান প্রায় ১৪ দিন, শুক্রের প্রায় ৩ ১/২ মাস; কিন্তু পৃথিবীর অমাবস্যা ও পূর্ণিমার ব্যবধান হইবে প্রায় ৬ মাস।
শুক্রের দেহের বস্তুসমূহের আপেক্ষিক গুরুত্ব পৃথিবীর চেয়ে সামান্য কম। পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্ব ৫.৫২ এবং শুক্রের ৫.২১। ওজনে শুক্র পৃথিবীর ওজনের ১০০ ভাগের ৮১ ভাগের সমান। পৃথিবী ও শুক্রের নিষ্ক্রমণ বেগের ব্যবধান অল্পই। পৃথিবীর ৭ ও শুক্রের ৬ ১/২ মাইল। শুক্রের তাপ পৃথিবীর তাপের চেয়ে অনেক বেশি। যেহেতু শুক্র আছে পৃথিবীর চেয়ে সূর্যের ২ কোটি ৫৭ লক্ষ মাইল নিকটে। অধিকন্তু শুক্রে জলের নামগন্ধও নাই। যেহেতু সেখানে এখনও জলের সৃষ্টি হয় নাই। শুক্রে বাতাস আছে। কেননা শুক্রের নিষ্ক্রমণ বেগ অতিক্রম করিয়া এক কণা বাতাসও মহাকাশে পালাইতে পারে নাই। কিন্তু উহার সবই কার্বন-ডাই-অক্সাইড, সেই বাতাসে আঁটি অক্সিজেন মোটেই নাই। ইহার কারণ এই যে, শুক্রে গাছপালা নাই। উদ্ভিদেরাই কার্বন-ডাই অক্সাইড হইতে অক্সিজেন প্রস্তুত করে। আর যেখানে অক্সিজেন নাই, সেখানে কোনো জীবের অবস্থানও অসম্ভব।
বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, দূর ভবিষ্যতে শুক্রের দেহের তাপ কমিয়া পৃথিবীর তাপের কাছাকাছি হইলে সেখানে জলের অণুর সৃষ্টি হইবে এবং উদ্ভিদাদির জন্ম হইবে। তৎপর শুক্রের বাতাসে অক্সিজেনের সৃষ্টি হইলে জীবোৎপত্তির সম্ভাবনাও আছে। তবে তাহা কয়েক শত কোটি বৎসর পরের কথা। শুক্র আছে বর্তমান পৃথিবীর প্রায় আড়াই শত কোটি বৎসর আগের অবস্থায়।
পৃথিবীর তুলনায় শুক্র গ্রহের বর্তমান অবস্থা খুবই নিকৃষ্ট। কিন্তু ধর্মজগতে উহার কদর যথেষ্ট। শুক্রবারের আরাধনায় নাকি পুণ্য বেশি হয় এবং ঐদিন নাকি স্বর্গের দ্বার খোলা এবং নরকের দ্বার বন্ধ থাকে। পৌরাণিক মতে, শুক্র নাকি দৈত্যগণের গুরু। ইহার পিতার নাম ভৃগু, তাই ইহার অপর নাম ভার্গব। আবার মতান্তরে –মহেশ্বরের উপস্থ (শিবের লিঙ্গ) দ্বার হইতে বহির্গত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে শুক্র। ইহার ছেলেমেয়ে তিনটি। ছেলের নাম ষণ্ড ও অমর্ক এবং মেয়ের নাম দেবযানী। বলি রাজার দানে ব্যাঘাত করায় ইহার একটি চক্ষু নষ্ট হয়।
এই জন্য ইহার সাধারণ নাম কাণা শুক্র। সে যাহা হউক, এই সকল বাক্যালকার চটকদার বটে, কিন্তু ইহা এখন বিজ্ঞানের বাজারে বিকায় না।
.
# ৩. পৃথিবী
ধর্মীয় মতে, পৃথিবী ঈশ্বরের এরূপ একটি বিশেষ সৃষ্টি, যাহার সমতুল্য সৃষ্টিরাজ্যে আর কিছুই নাই। কিন্তু বিজ্ঞানীগণ তাহা বলেন না। তাহারা বলেন যে, পৃথিবী নবগ্রহের একটি গ্রহ মাত্র। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহদের মধ্যে আকৃতি ও প্রকৃতিতে বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই। এই বিষয়ে বিজ্ঞানীগণ যাহা বলেন, তাহার কিছু আলোচনা করিতেছি।
মেরু –পৃথিবী গোল, অথচ উত্তর ও দক্ষিণ দিকে কিঞ্চিৎ চাপা। দেখা যায় যে, অন্যান্য গ্রহের আকৃতিও ঐরূপ। যথা– পৃথিবীর ব্যাস বিষুবীয় অঞ্চলে ৭,৯২৬ মাইল ও মেরু অঞ্চলে ৭,৯০০ মাইল। ঐরূপ বৃহস্পতির ব্যাস বিষুবীয় অঞ্চলে ৮৮,৭০০ মাইল ও মেরু অঞ্চলে ৮২,৭৮০ মাইল, শনির ব্যাস বিষুবীয় অঞ্চলে ৭৫,০৬০ মাইল ও মেরু অঞ্চলে ৬৭,১৬০ মাইল ইত্যাদি।
আয়তন –গ্রহদের আয়তনে ব্যবধান যথেষ্ট আছে। কিন্তু তাহা অতুলনীয় নহে। বুধ গ্রহের আয়তন পৃথিবীর আয়তনের প্রায় ১৭ ভাগের এক ভাগের সমান। কিন্তু বৃহস্পতি পৃথিবী হইতে প্রায় ১৩ শত গুণ বড়। পক্ষান্তরে শুক্র ও পৃথিবীর আয়তন প্রায় সমান। অর্থাৎ ৯ ও ১০-এ পার্থক্য যতখানি, শুক্র ও পৃথিবীর আয়তনে পার্থক্য তাহার চাইতে বেশি নহে।
আহ্নিক গতি –একমাত্র বুধ গ্রহ ব্যতীত অপর সকল গ্রহেরই লক্ষ্যনীয় আহ্নিক গতি আছে। তবে শুক্র, পসিডন ও ভালকান গ্রহের আছে কি না, তাহা এখনও সঠিক জানা যায় নাই। আহ্নিক গতির ফলেই গ্রহরাজ্যে দিন ও রাত্রি হইয়া থাকে। কিন্তু সকল গ্রহের দিন-রাত্রির পরিমাণ সমান নহে। পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের চারিপাশে একবার ঘুরিয়া আসে ২৪ ঘণ্টায়, তাই পৃথিবীর দিন রাত্রির পরিমাণ ২৪ ঘণ্টা। এইরূপ মঙ্গল গ্রহের দিন-রাত্রির পরিমাণ ২৪ ঘন্টা ৩৭ মিনিট, বৃহস্পতির ১০ ঘণ্টা, শনির ১০ ঘণ্টা ১৬ মিনিট, ইউরেনাসের ১০ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট, নেপচুনের ১৫ ঘন্টা ৪০ মিনিট ইত্যাদি।
বার্ষিক গতি –বার্ষিক গতি গ্রহদের সকলেরই আছে। তবে তাহার সময় বিভিন্ন। যে গ্রহ সূর্যের যত নিকটে, কক্ষপথে চলিয়া সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে সেই গ্রহের সময় লাগে তত কম এবং দূরের গ্রহের সময় লাগে বেশি। এই বিষয়ে পৃথিবী তাহার প্রতিবাসী গ্রহদের সহিত তাল মিলাইয়া চলিতেছে। যথা– সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে শুক্রের সময় লাগে ২২৫ দিন, পৃথিবীর লাগে প্রায় ৩৬৫ দিন এবং মঙ্গলের এক পাক শেষ করিতে সময় লাগে ৬৮৭ দিন।
কক্ষপথে গতি –পূর্বে আলোচনা করিয়াছি যে, যে গ্রহের ভ্রমণপথ বা কক্ষ সূর্য হইতে যত দূরে, সেই গ্রহের চলন তত ধীর এবং যে গ্রহের কক্ষপথ সূর্যের যত নিকটে, সেই গ্রহের গতি তত দ্রুত। এই বেগকে বলা হয় চক্ৰবেগ। পৃথিবীর ভ্রমণপথ শুক্র ও মঙ্গলের কক্ষপথের মধ্যে অবস্থিত। কাজেই পৃথিবীর চক্রবেগ হওয়া উচিত শুক্র ও মঙ্গলের চক্রবেগের মাঝামাঝি। বস্তুত হইয়াছেও তাহাই। যথা –শুক্রের চক্রবেগ সেকেণ্ডে ২১.৭ মাইল এবং মঙ্গলের ১৫ মাইল; উভয়ের মাঝামাঝি পৃথিবীর ১৮.৫ মাইল।
কৌণিক অবস্থান –সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিবার সময় গ্রহগণ তাহাদের কক্ষপথ বা নিরক্ষবৃত্তের উপর সমান্তরালভাবে থাকে না, ঈষৎ হেলিয়া থাকে। পৃথিবীর বেলায়ও ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। যথা –পৃথিবী ২৩, মঙ্গল ২৫, বৃহস্পতি ৩, শনি ২৭ ও ইউরেনাস ৬০ ডিগ্রী কোণ করিয়া হেলিয়া আছে।[১৫]
উপগ্রহ –বুধ ও শুক্র গ্রহের কোনো উপগ্রহ নাই এবং লুটো, পসিডন ও ভালকানের আছে কি না, তাহা এখনও জানা যায় নাই। অপর সমস্ত গ্রহেরই উপগ্রহ বা চন্দ্র আছে। যথা– পৃথিবীর ১টি, মঙ্গলের ২টি, বৃহস্পতির ১২টি, শনির ৯টি, ইউরেনাসের ৫টি এবং নেপচুনের চন্দ্র আছে ২টি।
স্তর –পূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে, সৃষ্টির প্রাক্কালে পৃথিবীর ভারি পদার্থগুলি নিচের দিকে ও হাল্কা পদার্থগুলি উপরে থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন তিনটি প্রধান স্তরে সজ্জিত হইয়া আছে। সুতরাং ভূগর্ভে প্রধান স্তর তিনটি। যথা –কেন্দ্র হইতে গলিত ধাতু স্তর ২,২০০ মাইল, ব্যাসল্ট স্তর ১,৮০০ মাইল এবং উপরে গ্রানাইট স্তর ৩০ মাইল। অনুরূপভাবে অন্যান্য গ্রহেরও স্তরভেদ আছে। যথা –বৃহস্পতির কেন্দ্র হইতে ২২ হাজার মাইল পাথর স্তর, ১৬ হাজার মাইল বরফ স্তর ও ৬ হাজার মাইল বায়ু স্তর; ইউরেনাসের কেন্দ্র হইতে ৭ হাজার মাইল পাথর স্তর, ৬ হাজার মাইল বরফ স্তর এবং প্রায় ৩ হাজার মাইল বায়ু স্তর ইত্যাদি।[১৬]
নিষ্ক্রমণ বেগ –পৃথিবীর নিষ্ক্রমণ বেগ ৭ মাইল। এইখানে যদি কোনো পদার্থ প্রতি সেকেণ্ডে ৭ মাইল অর্থাৎ ঘণ্টায় ২৫,২০০ মাইল গতিবেগ অর্জন করিতে পারে, তবে উহাকে পৃথিবী তাহার মাধ্যাকর্ষণী শক্তির দ্বারা টানিয়া রাখিতে পারে না, উহা মহাকাশে চলিয়া যায় বা চাঁদের মতো এক কক্ষপথে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। এই নিয়মের ভিত্তিতেই বিজ্ঞানীগণ আজকাল পরিচালনা করিতেছেন রকেটের সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহ। অনুরূপ অন্যান্য গ্রহেরও ভিন্ন ভিন্ন রকম নিষ্ক্রমণ বেগ আছে। যথা –বুধের ২.৪, শুক্রের ৬.৫, মঙ্গলের ৩.২ ও বৃহস্পতির ৩৮.০ মাইল ইত্যাদি।[১৭]
ভূপৃষ্ঠের তাপ পরিমিত ও সহনীয়। কাজেই এইখানে জলবায়ুর সৃষ্টি হইতে পারিয়াছে এবং পৃথিবীর নিষ্ক্রমণ বেগ বেশি বলিয়া উহার সমস্তই সে ধরিয়া রাখিতে পারিয়াছে, তাই এইখানে জীবনের সৃষ্টি ও জীবের বসবাস সম্ভব হইয়াছে।
পৃথিবীর চাঁদ
আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে সূর্য ভিন্ন দৃশ্যত চন্দ্ৰই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উজ্জ্বল। বস্তুত চন্দ্র একটি অনুজ্জ্বল পদার্থ এবং আয়তনেও বেশি বড় নহে। চন্দ্রের ব্যাস মাত্র ২,১৬০ মাইল। অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় এক-চতুর্থাংশের সমান। তথাপি চন্দ্রকে এতোধিক বড় দেখাইবার কারণ এই যে, অন্যান্য জ্যোতিষ্কের তুলনায় চন্দ্র পৃথিবীর অতি নিকটে অবস্থিত। চন্দ্রের নিজের কোনো আলো নাই। সূর্যালোক পতিত হইবার ফলেই উহাকে উজ্জ্বল দেখায় এবং আমরা যে চন্দ্রালোক পাইয়া থাকি, আসলে উহা চন্দ্রের আলো নহে; উহা প্রতিফলিত সূর্যালোক। অর্থাৎ চন্দ্রপৃষ্ঠে ঠিকরানো সূর্যালোক।
সেকালের লোকে চন্দ্রকে লইয়া কতরকম কাহিনীই না রচনা করিয়াছেন। চন্দ্রের কলককে কেহ বলিয়াছেন হরিণশিশু, কেহ বলিয়াছেন, ‘চাঁদের মা সুতা কাটিতেছে’ ইত্যাদি। কোনো কোনো মতে, চন্দ্রের সংখ্যা বারোটি। অর্থাৎ বারো মাসে বারো চাঁদ।
হিন্দুদের পুরাণ-শাস্ত্রমতে চন্দ্র অত্রি ঋষির পুত্র (মতান্তরে সমুদ্রমন্থনে ইহার জন্ম)। ইনি দশটি কুন্দধবল অশ্ব বাহিত রথে আকাশভ্রমণ করেন। ইনি দক্ষরাজের ২৭টি কন্যাকে বিবাহ করেন। স্ত্রীদের প্রতি অবিচার করায় তাহারা দক্ষরাজের নিকট নালিশ করিলে তিনি যে আদেশ দেন, তাহা অমান্য করায় দক্ষরাজের অভিশাপে চন্দ্র যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হন এবং প্রভাসতীর্থে গিয়া শ্বশুরের আদেশ পালন করিয়া রোগমুক্ত হন। প্রবাদ আছে যে, চন্দ্র বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে হরণ করেন এবং তাহার গর্ভে বুধ জন্মলাভ করেন (এই মতে বুধ তারার গর্ভজাত সন্তান, তবে জারজ)।
জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, নীহারিকা, নক্ষত্র বা গ্রহ-উপগ্রহরা সকলেই যেন ব্যোমসমুদ্রের মাঝে এক একটি দ্বীপ। সে হিসাবে আমাদের চন্দ্রও ব্যোমসাগরের একটি দ্বীপ। ইহাকে বলা যাইতে পারে চন্দ্রদ্বীপ। তবে বঙ্গদেশের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ‘বাকলা চন্দ্রদ্বীপ’ নহে, ইহা আসল চন্দ্রদ্বীপ। কেননা বাকলার ‘চন্দ্রদ্বীপ’ নামটির সৃষ্টি হইয়াছিল উহার আবিষ্কর্তা চন্দ্ৰকান্তের নামানুসারে, মতান্তরে ঐ দ্বীপটির আকৃতি চন্দ্রের ন্যায় ছিল বলিয়া, অর্থাৎ চন্দ্ৰকান্তের দ্বীপ বা চন্দ্রের ন্যায় দ্বীপ। আর বিজ্ঞানীদের মতে চন্দ্র প্রকৃতই একটি দ্বীপ।
চন্দ্র যে রজত-কাঞ্চন বা হীরা-মুক্তার তৈয়ারী অথবা স্বর্গীয় মাহাত্মপূর্ণ আজগুবি কিছু নহে, উহা আমাদের পৃথিবীর মতোই একটি দেশ মাত্র, বিজ্ঞানীগণ ইহা বহু আগে হইতেই জানিতেন। এবং গাণিতিক ও যান্ত্রিক উপায়ে উহার বহু তথ্যও সংগ্রহ করিয়াছেন। সম্প্রতি বিজ্ঞানীগণ সফল হইয়াছেন চন্দ্র অভিযানে। নিরাপদে ও নিয়মিতভাবে চন্দ্রে যাতায়াত আরম্ভ হইলে পর, উহার ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক বহু নূতন তথ্য জানা যাইবে। হয়তোবা কোনো কোনো বিষয়ে পুরাতন তথ্যেরও কিছু কিছু সংশোধন আবশ্যক হইতে পারে। যেমন, পূর্বে বলা হইয়াছে পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব ২ লক্ষ ৩৯ হাজার মাইল, আর অধুনা জানা যাইতেছে যে, পৃথিবীর কেন্দ্র হইতে চন্দ্রের কেন্দ্রের দূরতম দূরত্ব ২,৫২,৭১০. মাইল এবং নিকটতম দূরত্ব ২,২১,৪৬৩ মাইল, অর্থাৎ গড় দূরত্ব ২,৩৭,০৮৬২ মাইল ইত্যাদি। বিজ্ঞানীদের চন্দ্রাভিযান প্রচেষ্টা সবেমাত্র সফল হইয়াছে। চন্দ্রের যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের এখনও অনেক বাকি। চন্দ্রাভিযানের এই যুগসন্ধিক্ষণে চাঁদের দেশের পুরাতন তথ্যের বেশি আলোচনা না করিয়া প্রত্যক্ষদর্শী বিজ্ঞানীদের বিবরণের প্রতীক্ষায় রহিলাম।
চাঁদে অবতরণ
বহুদিন হইতে বিজ্ঞানীগণ চাঁদে যাইবার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। চন্দ্রাভিযানের প্রথম পর্বের অগ্রদূত ছিলেন রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা। কিন্তু কেন যেন অবতরণ পর্বে তাহারা পিছাইয়া পড়িলেন, অগ্রগামী হইলেন আমেরিকান বিজ্ঞানীগণ। ১৯৬৯ সাল হইতে এই পর্যন্ত তাহারা চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করিয়াছেন ছয়বার। সেই অবতরণসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হইল।
মানুষের চন্দ্রাভিযান সফল করিবার প্রথম গৌরব অর্জন করেন নভোশ্চর-বিজ্ঞানী আর্মস্ট্রং, আলড্রিন ও কলিনস্। উঁহারা ভূপৃষ্ঠ হইতে চন্দ্রাভিমুখে যাত্রা করিয়া ১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই চন্দ্রে অবতরণ ও ভ্রমণ শেষে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসেন ২৪ জুলাই। উঁহারা চন্দ্রপৃষ্ঠ হইতে নানা স্থানের ফটো ও কিছু মাটি-পাথর লইয়া আসেন এবং সেখানে রাখিয়া আসেন আমেরিকান ফ্ল্যাগ, বাইবেল ও বিয়ারের খালি বোতল। আর ভুলবশত ফেলিয়া আসেন একটি ক্যামেরা।
২য় বার –এইবারের অভিযাত্রী ছিলেন কনার্ড, গর্ডন ও বীন। উঁহারা ভূপৃষ্ঠ হইতে যাত্রা করেন ১৯৬৯ সালের ১৪ নভেম্বর, অবতরণ করেন ১৯ এবং পৃথিবীতে ফিরিয়া আসেন ২৪ নভেম্বর। উঁহারা রকেট বা চন্দ্রযানে একখানা গাড়ি লইয়া যান এবং উহাতে আরোহণ করিয়া চন্দ্রপৃষ্ঠে ভ্রমণ করেন ও গাড়িখানা সেখানে রাখিয়া আসেন।
৩য় বার –এইবারের অভিযাত্রী ছিলেন লভেল, হেইজ ও সুগার্ড। উঁহারা গিয়াছেন ১৯৭০ সালের ১৮ এপ্রিল এবং আনিয়াছেন চন্দ্রপৃষ্ঠের নানা স্থানের ফটো।
৪র্থ বার –এইবারের অভিযাত্রী শেফার্ড, রূসা ও মিচেল। উঁহারা গিয়াছিলেন ১৯৭১ সালের ৩০ জানুয়ারি।
৫ম বার –এইবারের অভিযাত্রী শেরম্যান, ইভা ও স্মিথ। উঁহারা গিয়াছিলেন ১৯৭২ সালের ৮ ডিসেম্বর।
৬ষ্ঠ বার –এইবারে যান স্ট্যাফোর্ড, স্লেটন ও ব্ৰাণ্ড। উঁহারা গিয়াছিলেন ১৯৭৫ সালের ২৬ জুলাই তারিখে।
[ পিয়ার্স সাইক্লোপিডিয়া, ৮০তম এডিশন; পৃ. এ ৩৩ –এ ৩৬ ]
অভিযাত্রীগণ চন্দ্রপৃষ্ঠ হইতে যে মাটি, পাথর, ফটো ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, সেই। সবের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিতেছে, ফলাফল এখনও সাধারণ মানুষের অজ্ঞাত। তবে চাঁদের মাটি পরীক্ষা করিয়া বিজ্ঞানীগণ জানিতে পারিয়াছেন যে, চাঁদের বয়স পৃথিবীর বয়সের সমান। অর্থাৎ প্রায় ৫০০ কোটি বৎসর। চাঁদে জল, বায়ু ও কোনোরূপ জীবের অস্তিত্ব নাই এবং অতীতে কোনোরূপ জীব থাকারও কোনো নিদর্শন নাই। আগামীতে যদি জানা যায় যে, চাঁদের রাজ্যে এমন কোনো পদার্থ আছে, যাহা মানব জাতির পক্ষে কল্যাণকর, তবে সেইটিই হইবে চাঁদের বাস্তব ফজিলত। ধর্মীয় তথাকথিত চাঁদের ফজিলত এখন অচল।
.
# ৪. মঙ্গল
মঙ্গল সৌরজগতের চতুর্থ গ্রহ। পৃথিবীর ভ্রমণপথের বাহিরেই মঙ্গলের ভ্রমণপথ। কাজেই মঙ্গল পৃথিবীর প্রতিবেশী। সূর্য হইতে ইহার মোটামুটি দূরত্ব ১৪ কোটি ১৭ লক্ষ মাইল। কক্ষভ্রমণের সময়ে সূর্য হইতে মলের দূরত্ব কোনো সময় হয় ১২ কোটি ৮০ লক্ষ মাইল ও কোনো সময়ে হয়। ১৫ কোটি ৫০ লক্ষ মাইল।
মঙ্গলের ব্যাস ৪,২১৬ মাইল এবং আয়তনে মঙ্গল পৃথিবীর বিশ ভাগের তিন ভাগের সমান। মঙ্গলের ভ্রমণপথ পৃথিবীর ভ্রমণপথ হইতে কিছু বড় এবং মঙ্গলের চলনও কিছু ধীরগতি। স্বীয় কক্ষে পৃথিবী চলে সেকেণ্ডে ১৮ ১/২ মাইল। কিন্তু মঙ্গল চলে মাত্র ১৫ মাইল। তাই একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে মঙ্গলের সময় লাগে ৬৮৭ দিন। অর্থাৎ মঙ্গলের এক বৎসর আমাদের পৃথিবীর প্রায় দুই বৎসরের সমান। মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবার পাক দিতে মঙ্গলের সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা ৩৭ ১/২ মিনিট। সুতরাং মঙ্গলের দিন-রাত পৃথিবীর দিন-রাতের চেয়ে ৩৭ ১/২ মিনিট বড়।[১৮]
ফোবো ও ডাইমো নামে মঙ্গলের দুইটি উপগ্রহ বা চন্দ্র আছে। ফোবো মঙ্গলের ৫,৮২৮ মাইল দুরে থাকিয়া ৭ ঘণ্টা ৪০ মিনিট ৪৮ সেকেণ্ডে একবার মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। অর্থাৎ মঙ্গলের আকাশে ফোবোর অমাবস্যা বা পূর্ণিমা হয় দৈনিক তিনবার। ডাইমো আছে মঙ্গল হইতে ১৫ হাজার মাইল দূরে এবং মঙ্গলকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে তাহার সময় লাগে ৩০ ঘণ্টা ১৪ মিনিট ২৪ সেকেণ্ড। পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে আমাদের চাঁদের যেখানে সময় লাগে ২৯ দিন ১২ ঘন্টা ৪৪.০৫ মিনিট, অর্থাৎ প্রায় ৩০ দিন, সেখানে ডাইমোর সময় লাগে মাত্র ৩০ ঘণ্টা। আমাদের চাঁদের অমাবস্যা ও পূর্ণিমার মাঝখানের অন্তর প্রায় ১৫ দিন, কিন্তু ডাইমোর অমাবস্যা ও পূর্ণিমার অন্তর মাত্র ১৫ ঘণ্টা। কাজেই মঙ্গলের আকাশে প্রতিরাত্রে পূর্ণিমা তো আছেই, কোনো কোনো রাত্রে ডবল পূর্ণিমাও হইয়া থাকে। মঙ্গলের রাজ্যে যদি মানুষ থাকে, তবে তাহারা খোরাক পোশাক কি পরিমাণ পায় তাহা জানি না, কিন্তু চন্দ্রালোক আমাদের চেয়ে বেশিই পায়।
মঙ্গলের নিষ্ক্রমণ বেগ ৩.২ মাইল। এত অল্প নিষ্ক্রমণ বেগ সত্ত্বেও মঙ্গলে জলবায়ুর খবর পাওয়া যাইতেছে। জলবায়ু থাকিবার কারণ এই যে, মগলে তাপ কম। ভূপৃষ্ঠের গড় উত্তাপ প্রায় ৬৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট। কিন্তু মঙ্গলের উত্তাপ বিষুবাঞ্চলে দিনের বেলা ৫০ ডিগ্রী ফারেনহাইট বা তাহারও কিছু বেশি; আবার মধ্যরাত্রে নামিয়া যায় হিমাঙ্কেরও ১৩০ ডিগ্রী ফারেনহাইট নিচে। মঙ্গলের উত্তাপে দিনে ও রাত্রে এত পার্থক্য হইবার কারণ এই যে, মঙ্গলের বায়ুতে জলীয় অংশ নিতান্ত কম। পৃথিবীতে যেমন উপকূলীয় অঞ্চলের বায়ু সিক্ত বলিয়া সেখানে দিন ও রাত্রের উত্তাপে বিশেষ পার্থক্য হয় না, পক্ষান্তরে মরু অঞ্চলের বায়ু শুষ্ক বলিয়া সেখানে দিন ও রাত্রের উত্তাপে দারুণ পার্থক্য –ইহাও তেমনই।
মঙ্গলের আকাশে বায়ু খুব কম। তাহার মধ্যে আবার অক্সিজেন আছে নামমাত্র। মঙ্গলকে সহজ দৃষ্টিতে একটি উজ্জ্বল লাল রং-এর জ্যোতিষ্ক বলিয়া মনে হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেন যে, মঙ্গলের গায়ের লাল রংটি উহার পৃষ্ঠদেশের মরিচা ধরা পাথর বা বালিরই রং। শীতকালে মঙ্গলের মেরু অঞ্চল বরফে ঢাকা থাকে। তাই তখন মেরু অঞ্চলের রং হয় শাদা। গ্রীষ্মকালে মেরু অঞ্চলের শাদা রং থাকে না এবং বিষুবীয় অঞ্চলের রং হয় সবুজ। মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশে অনেক কালো কালো রেখা দেখা যায়, কোনো কোনো বিজ্ঞানী ঐগুলিকে বলেন মঙ্গলের নদী বা খাল। গ্রীষ্মকালে মেরু অঞ্চলের বরফ গলা জল ঐ সকল খাল বা নদীপথে আসিয়া বিষুবীয় অঞ্চল সিক্ত করিলে মওশুমী উদ্ভিদ জন্মে এবং তখন মঙ্গলের গাত্রে সবুজ আভা ফুটিয়া উঠে।
সৃষ্টির আদিতে মঙ্গলের দেহের তাপ সূর্যের বহিরাবরণের তাপের সমান ছিল, অর্থাৎ ৬ হাজার ডিগ্রী সে.। কোটি কোটি বৎসরে ঐ বিপুল তাপের সম্বল হারাইয়া বর্তমানে মঙ্গলের তাপ দাঁড়াইয়াছে মাত্র ৫০° ফারেনহাইটে। সুতরাং মঙ্গল এখন মরণপথের যাত্রী।
মঙ্গল গ্রহে উচ্চ শ্রেণীর কোনো জীব আছে কি না, তাহার কোনো সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মঙ্গল গ্রহে জল আছে, অল্প হইলেও বাতাস আছে এবং খুব সামান্য থাকিলেও তাহাতে অক্সিজেন আছে; কাজেই সেখানে জীব থাকা সম্পূর্ণ অসম্ভবও নহে। অধিকন্তু বিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, মঙ্গলের তাপ যখন পৃথিবীর বর্তমান তাপের সমান ছিল, তখন কোনো না কোনোরূপ জীব ও উদ্ভিদাদিতে মঙ্গল সুশোভিত ছিল। হয়তোবা তখন মঙ্গলের সাগরে মাছ, আকাশে পাখি ও স্থলে নানারূপ জীব বিচরণ করিত এবং অনুকূল অবস্থাপ্রাপ্ত হইলে শুক্রগ্রহেও জীবের আবির্ভাব হইয়া গ্রহটি জীবে পূর্ণ হইতে পারে। পৃথিবীর বর্তমান অবস্থা শুক্রের রাজ্যে ভবিষ্যত কিন্তু মঙ্গলের রাজ্যে অতীত।
.
# ৫. বৃহস্পতি
সূর্য হইতে বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গলের মোটামুটি দূরত্ব যথাক্রমে ৩, ৬, ৯ ও ১৪ কোটি মাইল। ইহাতে দেখা যায় যে, যে কোনো দুইটি গ্রহের ব্যবধান ৫ কোটি মাইলের বেশি নহে। সুতরাং সূর্য হইতে বিশ, পঁচিশ কিংবা ত্রিশ কোটি মাইলের মধ্যে আর একটি গ্রহ থাকা উচিত। কিন্তু জ্যোতির্বিদগণ দেখিলেন যে, একদম ৪৮ কোটি ৩৯ লক্ষ মাইল দূরে যাইয়া আছে বৃহস্পতি গ্রহ। বিজ্ঞানীগণ ভাবিলেন যে, মঙ্গল ও বৃহস্পতির ভ্রমণপথের মাঝখানে এত বড় একটি ফাঁকা জায়গা থাকিবার কোনো কারণ নাই। সুতরাং সেখানে নিশ্চয়ই একটা কিছু আছে।
পর্যবেক্ষণে প্রথম ধরা পড়িল দুই একটি বস্তুপিণ্ড, যাহা আমাদের চাঁদের চেয়ে বড় নহে। জ্যোতির্বিদগণ ভাবিলেন যে, উহারা উপগ্রহ। পর্যবেক্ষণ চলিতে লাগিল এবং ক্রমে ধরা পড়িতে লাগিল ঐ দলের ছোট হইতে ছোটরা। আকারে উহারা কোনোটি হিমালয় পর্বতের মতো বড়, কোনোটি আবার ত্রিতলা দালানের মতো। কিন্তু আকৃতি উহার কোনোটিরই সম্পূর্ণ গোল নহে। আকৃতিতে উহারা যেন ভাঙ্গা মার্বেলের এক একটি টুকরা।
বিজ্ঞানীগণ স্থির করিলেন যে, মঙ্গল ও বৃহস্পতির ভ্রমণপথের মধ্যে এককালে একটি মাঝারি ধরণের গ্রহ ছিল। হয়তো বৃহস্পতির টানে গ্রহটি ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছে। উহাদের মধ্যে যেগুলি আকারে বড়, সেগুলি দূরবীনে প্রথমেই ধরা পড়িয়াছে ও অপেক্ষাকৃত ছোটগুলি ক্রমে ধরা পড়িতেছে। কিন্তু অতি ছোট টুকরাগুলি হয়তো কোনোকালেই দৃষ্টিগোচর হইবে না। এই দৃশ্যাদৃশ্য টুকরাগুলির একযোগে নাম রাখা হইয়াছে গ্রহাণুপুঞ্জ বা গ্রহকণিকা। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝে নির্দিষ্ট কক্ষে থাকিয়া গ্রহকণিকারা সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে।
গ্রহকণিকাদের বাদ দিলে সৌররাজ্যে বৃহস্পতি পঞ্চম গ্রহ। সূর্য হইতে ইহার মোটামুটি দূরত্ব ৪৮ কোটি ৩৯ লক্ষ মাইল। বৃহস্পতির ব্যাস বিষুব অঞ্চলে ৮৮,৭০০ ও মেরু অঞ্চলে ৮২,৭৮০ মাইল। আয়তনে বৃহস্পতি পৃথিবী অপেক্ষা ১,৩১২ গুণ বড়।[১৯]
বৃহস্পতি আপন কক্ষপথে চলে সেকেণ্ডে ৮.১ মাইল বেগে। এইরূপ বেগে চলিয়া একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে তাহার সময় লাগে ১১.৮৬২ বৎসর। অর্থাৎ বৃহস্পতির এক বৎসর আমাদের প্রায় ১২ বৎসরের সমান।
আমাদের পৃথিবীর চন্দ্র আছে একটি এবং মঙ্গলের আছে দুইটি। কিন্তু বৃহস্পতির চন্দ্র আছে। বারোটি। নিকটের চন্দ্রটির নাম আইও। এইটি বৃহস্পতি হইতে ২ লক্ষ ৬১ হাজার মাইল দূরে থাকিয়া ১.৭৭ দিনে একবার বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। অর্থাৎ প্রায় ৪২ ঘণ্টায় আইওর একবার অমাবস্যা ও একবার পূর্ণিমা হইয়া থাকে। বৃহস্পতির দ্বিতীয় চন্দ্রটির নাম ইওরোপা। এইটি বৃহস্পতির ৪ লক্ষ ১৫ হাজার মাইল দূরে থাকিয়া ৩.৫৫ দিনে একবার বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ ইওরোপা একবার অমাবস্যা ও একবার পূর্ণিমা দেখায় প্রায় ৩ ১/২ দিনে। বৃহস্পতির বারোটি চাঁদের মধ্যে এগারোটির দূরত্ব জানা গিয়াছে। ইহার শেষ চাঁদটি আছে বৃহস্পতি হইতে ১,৪০,২৪,৮০০ মাইল দূরে এবং ৬৯২.৫ দিনে একবার বৃহস্পতিকে প্রদক্ষিণ করে। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রায় দুই বৎসরের সমান ঐটির এক চান্দ্রমাস।[২০]
দেখা যায় যে, খুব মোটা মানুষের গায়ের ওজন তত বেশি হয় না। বৃহস্পতিরও সেই দশা। আয়তনের বিশালতায় বৃহস্পতি গ্রহকুলের রাজা বটে। কিন্তু তাহার ওজন তত বেশি নহে। পৃথিবীর বস্তুগুরুত্ব ৫.৫২। কিন্তু বৃহস্পতির বস্তুগুরুত্ব মাত্র ১.৩৪। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রায় এক চতুর্থাংশের সমান। তাই আয়তনে বৃহস্পতি ১,৩১২টি পৃথিবীর সমান হইলেও, ওজন মাত্র ৩১৭ গুণ।
বৃহস্পতির তাপ হিমাঙ্কেরও নিচে, জল আছে বরফের আকারে ও বাতাস আঁটি অক্সিজেনের পরিবর্তে নানাবিধ বিষাক্ত বাষ্পে পরিপূর্ণ। সুতরাং সেখানে কোনোরূপ জীব বা জীবনের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।
হিন্দুদের পুরাণমতে –বৃহস্পতি দেবগণের গুরু ও মন্ত্রী। ইনি অঙ্গিরা ঋষির পুত্র। ইঁহার স্ত্রীর নাম তারা। চন্দ্র তারাকে হরণ করিলে ইনি দেবগণের সহায়তায় চন্দ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করেন। আবার চন্দ্রও দৈত্যগণের সহায়তায় যুদ্ধে প্রস্তুত হয়। অবস্থা গুরুতর দেখিয়া ব্রহ্মা চন্দ্রের নিকট হইতে তারাকে আনিয়া ইহাকে অর্পণ করিলে যুদ্ধ স্থগিত হয়। অতঃপর বৃহস্পতির ঔরসে কচ ও ভরদ্বাজ নামে দুইটি পুত্রেরও জন্ম হয়। সে যাহা হউক, বর্তমান যুগে এই সমস্ত কাহিনী কীটদষ্ট পুরাণের পাতায় চাপা পড়িয়াই আছে।
.
# ৬. শনি
বৃহস্পতির ভ্রমণপথের বাহিরে শনির ভ্রমণপথ। সূর্য হইতে ইহার দূরত্ব ৮৮ কোটি ৭১ লক্ষ মাইল। শনি গ্রহের ব্যাস বিষুব অঞ্চলে ৭৫,০৬০ মাইল ও মেরু অঞ্চলে ৬৭,১৬০ মাইল। পৃথিবীর মতোই ইহার মেরুদেশ চাপা। বৃহস্পতিকে বাদ দিলে এত বড় গ্রহ সৌরাকাশে আর নাই। আয়তনে শনি ৭৩৪টি পৃথিবীর সমান।
বৃহস্পতির ভ্রমণপথের চেয়ে শনির ভ্রমণপথ বড় এবং শনি চলে সেকেণ্ডে মাত্র ছয় মাইল গতিতে। এইরূপ বেগে চলিয়া একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে শনির সময় লাগে ২৯.৪৫৮ বৎসর। অর্থাৎ শনির এক বৎসর আমাদের প্রায় সাড়ে ঊনত্রিশ বৎসরের সমান। শনি নিজ মেরুদণ্ডের চারিদিকে একবার পাক দিতে পারে ১০ ঘণ্টা ১৬ মিনিটে। সুতরাং দিন-রাতের পরিমাণ প্রায় সোয়া দশ ঘণ্টা মাত্র। শনি ও বৃহস্পতির দিন-রাতের পার্থক্য বেশি নহে, মাত্র ১৬ মিনিট। কিন্তু পৃথিবীর এক দিন শনির প্রায় আড়াই দিনের সমান।
শনির চাঁদ আছে নয়টি। উহারা ভিন্ন ভিন্ন দূরত্বে থাকিয়া বিভিন্ন সময়ে শনিকে প্রদক্ষিণ করে। খুব কাছের চাঁদটির নাম মিমাস, এইটি শনির ১ লক্ষ ১৭ হাজার মাইল দূরে থাকিয়া ০.৯৪ দিনে একবার শনিকে প্রদক্ষিণ করে। সুতরাং একদিনের মধ্যেই উহার অমাবস্যা ও পূর্ণিমা হইয়া যায়। সর্বশেষ চাঁদটির নাম ফিবি (Phoebe)। এইটি শনির ৮,০৫৪ হাজার মাইল দূরে থাকিয়া ৫৫০.৪৫ দিনে একবার শনিকে প্রদক্ষিণ করে। সুতরাং পৃথিবীর প্রায় দেড় বৎসরের সমান ফিবি’র এক চান্দ্রমাস।
নয়টি চাঁদ শনিকে ঘিরিয়া পাক খাইতেছে। ইহা ভিন্ন আর একটি পদার্থ শনিকে ঘিরিয়া আছে, উহাকে বলা হয় শনির বলয়। শনির দেহ হইতে কিছু দূরে গাড়ির চাকার মত একটি উজ্জ্বল পদার্থ সব সময়ই শনিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে।
জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, শনির একটি উপগ্রহ এককালে শনির খুব কাছাকাছি হইয়াছিল। তাই তাহার প্রবল আকর্ষণে ঐটি চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায় এবং বিচূর্ণ কণাগুলি উহার ভ্রমণপথে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। ভগ্ন উপগ্রহটির ন্যায় কণাগুলিরও গতিবেগ থাকায় উহারা শনির টানে তাহার পৃষ্ঠদেশে পতিত না হইয়া নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকিয়া শনিকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। কোটি কোটি কণা। ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া চলিতে থাকায় দূর হইতে আমরা উহাদিগকে বলয়ের আকারে দেখি।
শনির নিষ্ক্রণ বেগ সেকেণ্ডে ২৩ মাইল এবং তাপ হিমাঙ্কেরও ১৫৫° সে. নিচে। এই তাপে এতোধিক নিষ্ক্রমণ বেগ অর্জন করিয়া শনির কোনো বায়বীয় পদার্থই মহাশূন্যে ছুটিয়া পলাইতে পারে নাই। সুতরাং হাইড্রোজেনাদির সংমিশ্রণে শনির বায়ুমণ্ডল নিশ্চয়ই বিষাক্ত এবং জলের নাম পর্যন্ত নাই, আছে শুধু বরফ, সুতরাং সেখানে জীব বা জীবনের অস্তিত্ব নাই। শনি একটি নির্জীব গ্রহ।
হিন্দুশাস্ত্র মতে –সুর্যের ঔরসে তৎপত্নী ছায়ার গর্ভে শনির জন্ম হয়। যমের হিসাবলেখক কর্মচারী চিত্রগুপ্তের কন্যার সহিত শনির বিবাহ হয়। একদা তাহার স্ত্রীর সহিত ঝগড়া হইলে স্ত্রী তাহাকে এই বলিয়া অভিশাপ দেয় যে, সে যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, তাহাই বিনষ্ট হইবে। অতঃপর মহাদেবের পুত্র গণেশের জন্ম হইলে অন্যান্য দেবতার সহিত শনি গণেশকে দেখিতে যায় এবং দৃষ্টিপাত করিতেই গণেশের মুণ্ড উড়িয়া যায়। তৎক্ষণাৎ একটি হাতির মুণ্ড আনিয়া গণেশের স্কন্ধে লাগাইলে গণেশ বাঁচিয়া যায় এবং তাহাতে গণেশ ‘গজানন’ অর্থাৎ ‘হস্তিমুণ্ড’ হয়।
ঐ সকল কাহিনী গাঁজার পর্যায়ে পড়িলেও শাস্ত্রকারের কল্পনার মূল্য আছে এবং সেজন্য শাস্ত্রকার ধন্যবাদের পাত্র।
.
# ৭. ইউরেনাস
পূর্বে আলোচিত ছয়টি গ্রহ এবং পৃথিবীর একটি উপগ্রহ সম্বন্ধে আগেকার জ্যোতিষীদের কিছু কিছু তত্ত্ব জানা ছিল। বাকি গ্রহ-উপগ্রহগুলি দূরবীন তৈয়ারীর পরের আবিষ্কার। অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী দূরবীন আবিষ্কারের সাথে সাথে গ্রহ-উপগ্রহদের সংখ্যা বাড়িয়াছে, হয়তো ভবিষ্যতে আরও বাড়িতে পারে।
শনির ভ্রমণপথের বাহিরে ইউরেনাসের ভ্রমণপথ। ইহার ব্যাস ৩২,৮৮০ মাইল, পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় চারিগুণ। সূর্য হইতে ইহার দূরত্ব ১৭৮ কোটি মাইল এবং প্রতি সেকেণ্ডে ৪.২ মাইল বেগে চলিয়া ৮৪.০১ বৎসরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। অর্থাৎ ইউরেনাসের এক বৎসর পৃথিবীর প্রায় ৮৪ বৎসরের সমান। ইউরেনাস নিজ মেরুদণ্ডের উপরে একবার আবর্তিত হয় ১০ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে। সুতরাং ইউরেনাসের দিন-রাত শনির দিন-রাতের চেয়ে ২৯ মিনিট বড়।
এই পর্যন্ত ইউরেনাসের পাঁচটি চাঁদের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। নিকটবর্তী চাঁদটির নাম আরিয়েল। এই চাঁদটি ১ লক্ষ ২০ হাজার মাইল দূরে থাকিয়া প্রায় আড়াই (২.৫২) দিনে ইউরেনাসকে একবার প্রদক্ষিণ করে। দূরতম চাঁদটির নাম মিরাণ্ডা। এই চাঁদটির দূরত্ব কত, তাহা এখনও নিণীত হয় নাই। তবে ইউরেনাসকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে ইহার সময় লাগে প্রায় দেড় (১.৪০) দিন।
ইউরেনাসের দেহের বস্তুপুঞ্জের গড় গুরুত্ব ১.২৭ এবং আয়তন ৬৪টি পৃথিবীর সমান। কিন্তু ওজনে ইউরেনাস ১৫টি পৃথিবীর সমানও নহে, পৃথিবীর তুলনায় মাত্র ১৪.৭ গুণ।
ইউরেনাসের নিষ্ক্রমণ বেগ ১৪.০০ মাইল। ইহা পৃথিবীর নিষ্ক্রমণ বেগের দ্বিগুণ। সুতরাং ইউরেনাসের আকাশের কোনো বায়বীয় পদার্থের একটি অণুও ইউরেনাসকে ছাড়িয়া পলাইতে পারে নাই। ইহার তাপ হিমাঙ্কের ১৮০° সে. নিচে। কাজেই সেখানে একবিন্দু জলও নাই, সমস্তই বরফ হইয়া আছে।
ইউরেনাসের জলবায়ু মোটামুটি শনিগ্রহের জলবায়ুর অনুরূপ। সুতরাং সেখানে কোনোরূপ জীব থাকিতে পারে না।
.
# ৮. নেপচুন
ইউরেনাসের পরেই নেপচুনের ভ্রমণপথ। দূরত্ব সূর্য হইতে ২৭৯ কোটি ৭০ লক্ষ মাইল। আয়তনে নেপচুন ৬০টি পৃথিবীর সমান। আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৫৮ মাত্র। কাজেই আয়তনের তুলনায় নেপচুনের ওজন কম, প্রায় ১৭টি পৃথিবীর সমান (১৭.২)। প্রতি সেকেণ্ডে ৩.৪ মাইল পথ চলিয়া প্রায় ১৬৫ (১৬৫.৭৮৮) বৎসরে নেপচুন একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। সুতরাং পৃথিবীর ১৬৫ বৎসরের সমান নেপচুনের এক বৎসর। বৎসরটি এত বড় হইলেও নেপচুনের দিন-রাত পৃথিবীর দিন-রাতের চেয়ে ছোট, মাত্র ১৫ ঘণ্টা ৪০ মিনিট।[২১]
ট্রাইটান ও নেরেইড নামে নেপচুনের দুইটি চাঁদ আছে। প্রথমটি ২,২১,৫০০ মাইল দূরে থাকিয়া প্রায় পৌনে ছয় (৫.৮৮) দিনে নেপচুনকে একবার প্রদক্ষিণ করে। দ্বিতীয়টির কক্ষ পরিক্রমা ও দূরত্ব সঠিকভাবে এখনও জানা যায় নাই।
নেপচুনের নিষ্ক্রমণ বেগ ১৫.০০ মাইল; ইহা পৃথিবীর নিষ্ক্রমণ বেগের দ্বিগুণেরও বেশি। নেপচুনের তাপ ইউরেনাসের তাপের চেয়ে অনেক কম। কাজেই নেপচুনের জলবায়ুর প্রকৃতি ইউরেনাস বা শনি গ্রহের মতোই। সুতরাং সেখানে জীবের অস্তিত্ব নাই।
.
# ৯. প্লুটো
ইহার দূরত্ব সূর্য হইতে ৩৬৭ কোটি মাইল। সেকেণ্ডে প্রায় তিন (২.৯) মাইল গতিতে চলিয়া প্রায় ২৪৮ (২৪৭.৬৯৭) বৎসরে লুটো একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। নেপচুনের রাস্তার চেয়ে লুটোর রাস্তা বড় এবং চলন ধীর। তাই আমাদের পৃথিবীর প্রায় ২৪৮ বৎসরের সমান পুটোর এক বৎসর। পৃথিবীতে যাহার বয়স ২০ বৎসর, প্লুটোর রাজ্যে তাহার বয়স এক মাসেরও কিছু কম।
প্লুটো গ্রহটি আছে সৌরজগতের দূর প্রান্তে এবং আকারও তাহার বেশি বড় নহে। এই দুই কারণে পুটো সম্বন্ধে বেশি কিছু বিজ্ঞানীরা এখনও জানিতে পারেন নাই। অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী দূরবীনের আবিষ্কার হইলে প্লুটো সম্বন্ধে অনেক অজানা বিষয় জানা যাইবে। বিশেষত বিজ্ঞানীদের শুক্র ও মঙ্গলাভিযান সফল হইলে মহাবিশ্বের অনেক নূতন তথ্য অবগত হওয়া যাইবে।
.
# ১০. ভালকান ও ১১. পসিডন
বিগত কয়েক বৎসর যাবত প্লুটো গ্রহটিকেই সৌররাজ্যের সীমান্তের গ্রহ বলিয়া মনে করা হইত। ইদানিং তাহারও বাহিরে ভালকান ও পসিডন নামে আরও দুইটি গ্রহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সূর্য হইতে পসিডন গ্রহটির দূরত্ব প্রায় ৭১৭ কোটি ৯০ লক্ষ মাইল। সদ্য আবিষ্কৃত বলিয়া উহাদের সম্বন্ধে অন্যান্য কোনো তথ্য এখনও জানা যায় নাই। হয়তো অতিশয় দূরে অবস্থিত বলিয়া অন্যান্য গ্রহদের ন্যায় উহাদের সম্বন্ধে তত বেশি তথ্য কখনও জানা যাইবে না।
.
অন্যান্য
# ধূমকেতু ধূমকেতু মানে ধুয়ার নিশান। সাধারণ্যে উহা লেজওয়ালা তারা নামে পরিচিত। সৌরাকাশে উহার আবির্ভাব খুব বিরল। তাই উহা বার বার দেখা যায় না। পশু-পাখির জন্য কি না তাহা জানি না, আকাশে ধূমকেতুর উদয় মানুষের জন্য নাকি অমঙ্গলজনক। এতদ্বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্রে জানা যায়– যে ধূমকেতুর আকার ইন্দ্রধনুর ন্যায়, অথবা যাহার মস্তকে দুইটি বা তিনটি চূড়া থাকে, উহা সাতিশয় অনিষ্টদায়ক। যাহাদিগের দেহ হ্রস্ব ও প্রসন্ন, তাহারা তত অনিষ্টদায়ক নহে। আবার দক্ষিণদিকে ধূমকেতুর উদয় হইলে ঘোরতর অনিষ্ট হয়; অন্যদিকে উদিত হইলে তাদৃশ অনিষ্টকর হয় না। বলা বাহুল্য যে, এই সকল পৌরাণিক কাহিনীর এখন আর কোনো মূল্য নাই। ধূমকেতু সম্বন্ধে জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ যাহা বলেন, তাহার সামান্য আলোচনা করিতেছি।
খুব দক্ষ শিল্পীরও ইমারত গঠনান্তে দেখা যায় যে, ইট, সুরকি ইত্যাদি সংগৃহীত মাল-মশলার কিয়দংশ ইতস্তত ছিটকাইয়া-ছড়াইয়া পড়িয়া থাকে। দ্রুপ অখণ্ড নীহারিকাপুঞ্জ হইতে নক্ষত্ররাজি সৃষ্টির প্রাক্কালে উহার কিছু মাল-মশলা মহাকাশে ইতস্তত ছিটকাইয়া-ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং উহা এখনও মহাকাশে বিরাজ করিতেছে।
ঐ সকল ছুটকো পদার্থগুলি –অণু, কণা বা পিণ্ডাকারে ঝক বাধিয়া মহাকাশে ইতস্তত ভ্রমণ করিতেছে। উপগ্রহদের গতির উদ্দেশ্য হইল গ্রহকে প্রদক্ষিণ করা, গ্রহদের গতির উদ্দেশ্য হইল সূর্যকে প্রদক্ষিণ করা এবং সূর্য বা নক্ষত্রদের গতির উদ্দেশ্য হইল নক্ষত্র জগতের কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করা ইত্যাদি; কিন্তু ঐ সকল ছুটকো পদার্থগুলির গতির তেমন কোনো উদ্দেশ্য নাই। উহারা উদ্দেশ্যহীনভাবে মহাকাশে অন্ধের মতো ভ্রমণ করে। এইভাবে চলিতে চলিতে উহাদের কোনো কোনো ঝক কোনো কোনো সময়ে সৌরাকাশে প্রবেশ করে। তখন সূর্যের তাপের প্রভাবে ঋকের অণু-কণাগুলির মধ্যে চঞ্চলতা দেখা দেয় এবং চঞ্চলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে ঠোকাঠুকির ফলে কতক অণু-কণা ভাঙ্গিয়া বাষ্পীয় আকার ধারণ করে। আঁকের বস্তুপিণ্ডগুলি চলিবার সময় বাষ্পীয় পদার্থটিকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারে না, উহা পিছনে পড়িয়া থাকে। সূর্যালোকে আমরা ঐ অণু, কণা বা বস্তুপিণ্ডের সমষ্টিকে দেখি ধূমকেতুর মুণ্ডরূপে এবং বাষ্পীয় অংশকে বলি লেজ। কোনো বিশেষ কারণে ধূমকেতুর লেজটি সব সময়ই সূর্যের বিপরীত দিকে থাকে।
সৌররাজ্য প্রবেশ করিলে সূর্যের আকর্ষণের ফলে ধূমকেতুর সরল গতি থাকে না, উহা বাকিয়া যায়। সূর্য হইতে উহার দূরত্বের কম-বেশি অনুসারে আকর্ষণের জোর কম বা বেশি হয়। আকর্ষণের জোর কম হইলে সূর্যকে অর্ধপ্রদক্ষিণ করিয়া, যেদিক হইতে আসিয়াছিল, চিরদিনের জন্য ধূমকেতুটি সেই দিকে চলিয়া যায় এবং আকর্ষণের জোর বেশি হইলে সূর্যের আকর্ষণের নাগপাশ ছিন্ন করিয়া যাইতে পারে না, এক পটলাকৃতি কক্ষপথে নির্দিষ্ট সময়ে সে বার বার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকে। ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, ধূমকেতুরা দুই ভাগে বিভক্ত; যাহারা একাধিক বার সৌরাকাশে প্রবেশ করে না, তাহারা হইল ‘পলাতক’ এবং যাহারা বার বার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, তাহারা হইল ‘বন্দী’।
সৌররাজ্যে বেড়াইতে আসিয়া কোনো কোনো ধূমকেতু ভালোয় ভালোয় ফিরিয়া যায়, আবার কেহবা চিরকালের মতো সূর্যের হাতে বন্দী হইয়া পড়ে। কিন্তু কোনো কোনো ধূমকেতুর বড়ই দুর্ভাগ্য। সৌররাজ্যে ভ্রমণ করিবার সময় যদি কোনো ধূমকেতু শনি, বৃহস্পতি বা অন্য কোনো বড় গ্রহের নিকট দিয়া যাইতে থাকে, তাহা হইলে সূর্য ও গ্রহের টানে ধূমকেতুটি আর আস্ত থাকে না, ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া ধূমকেতু নামটিই হারাইয়া ফেলে। এইভাবে যে-সব ধূমকেতু ধংস হইয়া যায়, তাহাদের দেহের ভগ্নাবশেষ তাহাদের চলতি পথে ইতস্তত ছড়াইয়া থাকে।
ধূমকেতু যখন দূরাকাশে থাকে তখন দূরবীনযোগে দেখিলে উহাকে এক টুকরা মেঘের মতো দেখায় এবং যতই সূর্যের নিকটবর্তী হইতে থাকে, ততই উহার উজ্জ্বলতা বাড়ে ও লেজ গজায়। সূর্যের নৈকট্যবৃদ্ধির সাথে সাথে ধূমকেতুর লেজও বৃদ্ধি পায়। সূর্য হইতে যতই দূরে যাইতে থাকে, ধূমকেতুর লেজ ততই ছোট হইতে থাকে ও শেষে অদৃশ্য হইয়া যায়। কোনো কোনো ধূমকেতুর লেজ লম্বায় ১০ কোটি মাইলেরও বেশি হইয়া থাকে। আবার কোনো কোনো ধূমকেতুর একাধিক লেজ দেখা যায়।
সূর্যের হাতে যে সকল ধূমকেতু বন্দী হইয়াছে, অন্য অন্য সময়ে সেইগুলি সৌররাজ্য হইতে এতই দূরে চলিয়া যায় যে, পুনঃ ফিরিয়া আসিতে একশত, দুইশত বা কোনো কোনো ধূমকেতুর সাত-আটশত বৎসর লাগিয়া যায়। অথচ ধূমকেতুর গতিবেগও নেহায়েত কম নহে, প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৮০০ মাইল। ১৬৮২ খ্রীস্টাব্দে হ্যাঁলি সাহেব একটি ধূমকেতুর গতিবিধি নির্ণয় করেন, তাই ঐটি ‘হ্যালির ধূমকেতু’ নামে পরিচিত। উক্ত ধূমকেতুটি প্রায় ৭৫ ১/২ বৎসর অন্তর একবার সৌরাকাশে উদিত হয়। ঐটি ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে শেষবারের মতো আমাদের আকাশে উদিত হইয়াছিল এবং প্রোক্ত হিসাবমতে আগামী ১৯৮৫ বা ৮৬ খ্রীস্টাব্দে আবার উদিত হইবার কথা।[২২]
আকৃতি দেখিয়া মনে হয় যে, ধুমকেতুর লেজ একটি বিরাট কিছু। বস্তুত তাহা নহে। উহা নিতান্ত হাল্কা বাষ্প মাত্র। বিজ্ঞানী জগদানন্দ রায় বলিয়াছেন, “সুবিধা হইলে গোটা ধূমকেতুর লেজ পকেটে পোরা যায় এবং উহা নিক্তিতে মাপিলে ওজন আধসের তিনপোয়ার বেশি হইবে না।” একবার একটি ধূমকেতুর লেজের ভিতর পৃথিবী ঢুকিয়া বেশ কিছুদিন কাটাইয়াছিল। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ তখন জানিতেই পারে নাই যে, তাহারা ধূমকেতুর লেজের ভিতর বাস করিতেছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, ধূমকেতুরা মানুষের কোনো ক্ষতি করে না বা করিতে পারে না। পৌরাণিক কাহিনীগুলি শাস্ত্রকারদের অলীক কল্পনা মাত্র।
.
# উল্কা
মেঘমুক্ত রাত্রির আকাশে দেখা যায় যে, হঠাৎ হাউই বাজির মতো একটি আলোর রেখা কিছুদূর যাইয়া মিলাইয়া গেল। সাধারণত ঐগুলিকে লোকে তারাখসা বলে। ছোটবেলায় মা-দিদিমার কাছে ঐসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিতেন, “এক জায়গায় থাকিয়া থাকিয়া যখন কোনো তারা অস্বস্তি বোধ করে, তখন সে ঘর বদল করে। চলিবার সময় উহার নাম বলিতে নাই, বলিলে সে যথাসময়ে স্থান পায় না এবং সত্বর স্থান লইতে না পারিয়া হঠাৎ ভূপতিত হইলে মানুষের অমঙ্গল ঘটিতে পারে।”
মা-দিদিমা অথবা ঠাকুরদাদারা যাহাই বলুন, আসলে ঐগুলি তারা নহে। উহারা হইল ছোট বড় নানা রকম বস্তুপিণ্ড। প্রশ্ন হইতে পারে যে, মহাকাশে ঐগুলির সৃষ্টি হইল কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানীগণ যাহা বলেন, তাহার কিছু আলোচনা করিব।
বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, সুদূর অতীতকালে কোনো নক্ষত্রের আকর্ষণের ফলে সূর্যের জ্বলন্ত বাষ্পীয় দেহের খানিকটা ছিন্ন হইয়া দূরান্তে গিয়া কুণ্ডলী পাকাইতে পাকাইতে পৃথিবীর জন্ম হয়। প্রথমত পৃথিবীও জ্বলন্ত বাম্পাকারে ছিল। ক্রমে শীতল হইয়া তরল অবস্থাপ্রাপ্ত হয়। কালক্রমে আরও শীতল হইয়া পৃথিবীর বহির্ভাগ কঠিন হইতে থাকে। কিন্তু তাহার অভ্যন্তরভাগ তরল অবস্থায়ই থাকে। পৃথিবীর বহিভাগ শীতল ও কঠিন হইয়া সঙ্কুচিত হইবার ফলে ভূগর্ভস্থ তরল পদার্থের উপর প্রবল চাপ পড়িতে থাকে। পৃথিবীর বহির্ভাগ দ্রুত শীতল হইয়া দ্রুত সকোচনের ফলে ভূগর্ভের তরল পদার্থের উপর যে পরিমাণ চাপ পড়িতে থাকে, অভ্যন্তরভাগের তরল পদার্থ দ্রুত তাপ ত্যাগ করিয়া ঐ পরিমাণ সঙ্কুচিত হইতে না পরিয়া সময় সময় পৃথিবীর বহিরাবরণ ভেদ করিয়া ফোয়ারার আকারে ছিটকাইয়া উর্ধে উঠিতে থাকে (এরূপ অত্যুষ্ণ তরল পদার্থের উদগীরণকে অগ্ন্যুৎপাত বলে এবং তাহার উৎসমুখে সৃষ্ট হয় আগ্নেয়গিরি)। সেকালে এইরূপ তরল পদার্থের উদগীরণ এত অধিক শক্তিসম্পন্ন হইত যে, উহা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ সীমার বাহিরে চলিয়া যাইত এবং মহাকাশের শীতল স্পর্শে শীতল হইয়া কঠিন পাথরের আকারপ্রাপ্ত হইত ও মহাকাশে ইতস্তত ভাসিয়া বেড়াইত।
কালক্রমে পৃথিবী আরও শীতল ও কঠিন হইয়া প্রাণীবাসের যোগ্য হইয়াছে এবং মহাকাশে ঐ ভাসমান পাথরগুলি আজও ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ঐসকল পাথরকে বলা হয় উল্কাপিণ্ড। উল্কাপিণ্ডগুলি ওজনে দুই-তিন ছটাক হইতে বিশ-পঁচিশ মণ বা ততোধিক ভারি হইয়া থাকে। উহারা মহাকাশে ভাসিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে কোনো কোনো সময় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের সীমার ভিতরে আসিয়া পড়ে এবং পৃথিবীর আকর্ষণের ফলে ভূপতিত হইতে থাকে। ভূপতিত হইবার সময় বায়ুর সংঘর্ষে উহারা প্রথমত উত্তপ্ত হয়, পরে জ্বলিয়া উঠে। যে সকল উল্কাপিণ্ড আকারে ছোট, তাহারা জ্বলিয়া মধ্যপথে নিঃশেষ হইয়া ভস্মে পরিণত হয় এবং যেগুলি আকারে বড়, তাহারা নিঃশেষ হইতে পারে না, উহারা আধপোড়া অবস্থায় সশব্দে ভূপতিত হয়। দহনের ফলে সাধারণত উহাদের রং কালো হইয়া থাকে।
পৃথিবীর গঠনোপাদান বা মৌলিক পদার্থের সংখ্যা ১০২টি। বিজ্ঞানীগণ উল্কার দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, উল্কার দেহের মৌলিক উপাদান উহারই মধ্যে ৫০টি। পৃথিবীতে নাই, এমন উপাদান উহাতে একটিও পাওয়া যায় নাই। বিশেষত বয়সেও উল্কারা পৃথিবীর সমবয়সী। সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, এই জাতীয় উল্কারা পৃথিবীরই অংশবিশেষ এবং এককালে ইহারা পৃথিবীতেই ছিল।
এই রকম কোনো উল্কাপিণ্ড লোকালয়ে পতিত হইলে লোকে উহা সংগ্রহ করিয়া সযত্নে রক্ষা করে। ঐরূপ সংগৃহীত আধপোড়া উল্কাপিণ্ড পাশ্চাত্যের প্রায় সকল যাদুঘরেই দেখিতে পাওয়া যায় এবং ভারতের কলিকাতা মিউজিয়মেও আছে বেশ কয়েকটি।
মক্কা শহরে পবিত্র কাবাগৃহে হেজরল আসোয়াদ নামে কালো রঙের একখানা পাথর রক্ষিত আছে। ঐ পাথরখানা নাকি আকাশ (স্বর্গ) হইতে পতিত হইয়াছিল। হাজীগণ উহাকে সসম্মানে চুম্বন করিয়া থাকেন। বোধ হয় যে, ঐ পাথরখানাও একখানা মাঝারি ধরণের উল্কা।
মহাকাশে বস্তুপিণ্ডের অভাব নাই। পূর্বোল্লিখিত কারণ ব্যতীত অন্যান্য কারণেও মহাকাশে বস্তুপিণ্ড জমিতে পারে এবং তাহা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আওতাধীনে আসিলে, তাহাতে উল্কাপাত হইতে পারে। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, সৌররাজ্যে আসিয়া যে সকল ধূমকেতুর অপমৃত্যু ঘটে, উহাদের দেহের বস্তুপিণ্ডগুলি উহাদের চলার পথে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকিয়া যায়। পৃথিবী তাহার স্বীয় কক্ষে চলিতে চলিতে বৎসরের কোনো কোনো দিন ঐরূপ মৃত ধূমকেতুর পথে হাজির হয় এবং ঐ বস্তুপিণ্ডগুলিকে কাছে পাইয়া টানিয়া ভূপাতিত করে। এইরূপ পতনোন্মুখ পিণ্ডগুলি জ্বলিয়া-পুড়িয়া উল্কার সৃষ্টি হয়। এই কারণেই বৎসরের বিশেষ কয়েকটি দিনে উল্কাপাত খুব বেশি হয়।
দিনে-রাতে পৃথিবীর আকাশে কতগুলি উল্কা প্রবেশ করিতেছে, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। দিবালোকে যে সকল উল্কাপাত হয়, তাহা প্রায়ই দেখা যায় না এবং রাত্রির উল্কাও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রগুলি থাকে দৃষ্টিসীমার বাহিরে। আমরা স্বচ্ছন্দে দেখিয়া থাকি মাত্র বড় বড় উল্কার পতন। একজন বিজ্ঞানী হিসাব করিয়া বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর আকাশে প্রতি ঘণ্টায় প্রায় ৪২ লক্ষ উল্কা প্রবেশ করে। আবার কোনোও বিজ্ঞানী হিসাব দেখাইয়াছেন যে, মহাশূন্য হইতে যে উল্কা পোড়া ছাই প্রতিদিন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে, তাহার পরিমাণ প্রায় এক হাজার টন।[২৩]
সচরাচর ৬০ মাইল হইতে ৮০ মাইল উপরে উল্কা দেখা যায় এবং ৪০ মাইলের নিচে উল্কা দেখা যায় না। যেগুলি আকারে ছোট, সেগুলি ৪০ মাইলের উপরেই জ্বলিয়া ভস্ম হইয়া যায়, ভূপতিত উদ্ধার সংখ্যা খুবই অল্প।
.
# কৃত্রিম গ্রহ ও উপগ্রহ
প্রকৃতি বা ঈশ্বরের সৃষ্ট গ্রহ-উপগ্রহাদির বিষয় আলোচনা করা হইল। অধুনা আকাশে আরও কতিপয় গ্রহ ও উপগ্রহ বিরাজ করিতেছে, যাহার সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর নহেন, মানুষ। তবে উহারা আকারে নেহায়েত ছোট। কিন্তু উহাদের উভয়ের প্রকৃতি একই। যেমন হস্তী ও পিপীলিকার আকারগত পার্থক্য থাকিলেও উহাদের প্রকৃতি বা জৈবধর্মে কোনো পার্থক্য নাই –ইহা তেমনই।
পূর্বে বলা হইয়াছে যে, পৃথিবীর নিষ্ক্রমণ বেগ ৭ মাইল। অর্থাৎ কোনো পদার্থ যদি প্রতি সেকেণ্ডে সাত মাইল গতিতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির বিপরীত দিকে ছুটিতে পারে, তবে পৃথিবী তাহাকে টানিয়া ফিরাইতে পারে না। অর্থাৎ সে আর কখনও মাটিতে পড়ে না। অতঃপর? বিজ্ঞানীগণ কল্পনা করিলেন যে, ঐ পদার্থটি মহাকাশে চলিয়া যাইবে এবং সে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকিবে। অর্থাৎ সে হইবে সূর্যের একটি নূতন বা কৃত্রিম গ্রহ। কিন্তু ঐ পদার্থটির গতি যদি সেকেণ্ডে ৭ মাইল না হইয়া ৫ মাইল হয়, তবে কি হইবে? বিজ্ঞানীরা স্থির করিলেন যে, ঐটি তখন পৃথিবীকে আবর্তন করিতে থাকিবে। অর্থাৎ সে হইবে পৃথিবীর একটি নূতন বা কৃত্রিম উপগ্রহ। এই বিষয়ে গবেষণা চালানো হইলে, উহাতে প্রথমে সাফল্য লাভ করিলেন রাশিয়ান ও পরে আমেরিকান বিজ্ঞানীরা।
.
# কৃত্রিম উপগ্রহ
স্পুটনিক ১
১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবর তারিখে স্পুটনিক ১ নামক একটি উপগ্রহ আকাশে প্রথম নিক্ষেপ করেন রাশিয়ার বিজ্ঞানীগণ। এলুমিনিয়ামের সঙ্গে অন্য ধাতুর সংমিশ্রণে ঐটি তৈয়ার হইয়াছিল। আকৃতি গোল, ব্যাস ২৩ ইঞ্চি, ওজন ছিল ১৮৪ পাউণ্ড। প্রতি সেকেণ্ডে ৫ মাইল অর্থাৎ ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল বেগে চলিয়া ৯৬.২ মিনিটে একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিত শুটনিক ১। কিন্তু উহার এই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা বেশিদিন স্থায়ী হয় নাই। কেননা, স্পুটনিক ১ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাহিরে উহার কক্ষপথ রচনা করিতে পারে নাই। ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় এক হাজার মাইল পর্যন্ত বায়ুর অস্তিত্ব আছে। কোনো উপগ্রহ ঐ এক হাজার মাইলের উর্ধে স্বীয় কক্ষপথ রচনা করিতে না পারিলে, বায়ুর সংঘর্ষে উহার গতি হ্রাস পাইতে থাকে এবং ক্রমে নিম্নগামী হইয়া বায়ুমণ্ডলের ঘন, স্তরে প্রবেশ করিলে বায়ুর সংঘাতে উহা ভাঙ্গিয়া বা উল্কার ন্যায় জ্বলিয়া-পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়। বায়ুমণ্ডলের ভিতরে কক্ষপথ থাকায় প্রথম স্পুটনিকের ঐ দশাই হইয়াছিল। বায়ুর সংঘর্ষহেতু ক্রমশ উহার গতিবেগ হ্রাস পাইবার ফলে নিম্নগামী হইয়া ঘন বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া এক সময় উহা ধংস হইয়া গিয়াছে। প্রথম স্পুটনিক আকাশে ছিল মাত্র ৯৬ দিন।
এক্সপ্লোরার
১৯৫৮ সালের ৩১ জানুয়ারি তারিখে আমেরিকার বিজ্ঞানীরা এই উপগ্রহটি আকাশে নিক্ষেপ করেন। পরিবহন রকেট সহ ইহার ওজন ছিল ৩০.৮ পাউণ্ড। রকেট বাদে এই উপগ্রহটির ওজন ১৮.১৩ পাউণ্ড, ব্যাস ৬ ইঞ্চি এবং রকেট লম্বায় ৬ ফুট ৮ ইঞ্চি। ইস্পাতে নির্মিত খোলের ভিতর রক্ষিত বিবিধ যন্ত্রপাতি। এক্সপ্লোরার একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে সময় লয় ১১৪ মিনিট। অর্থাৎ দৈনিক পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে প্রায় বারো বার।
কৃত্রিম গ্রহ-উপগ্রহদের কাহারও কক্ষপথ সম্পূর্ণ গোল নহে। ইহা সৌরাকাশের অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহদের মতোই ডিম্বাকার। তাই পৃথিবী প্রদক্ষিণের সময় এক্সপ্লোরার কোনো কোনো সময় ভূপৃষ্ঠের ২২০ মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়ে, আবার কোনো কোনো সময় চলিয়া যায় ১,৭০০ মাইল দূরে। আগেই বলা হইয়াছে যে, বায়ুমণ্ডলের গভীরতা প্রায় ১,০০০ মাইল। কাজেই এক্সপ্লোরার কোনো সময় বায়ুমণ্ডলের ভিতরে আসিয়া পড়ে এবং কোনো সময় চলিয়া যায় বাহিরে। সুতরাং উহাকে অনেক সময়ই বায়ুর বাধা ভোগ করিতে হয়। তাই এক্সপ্লোরারও পৃথিবীর আকাশে বেশিদিন থাকিতে পারিবে না। বিজ্ঞানীগণ অনুমান করেন যে, এক্সপ্লোরার উপগ্রহটি আকাশে থাকিয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকিবে ১০ বৎসর। অতঃপর সেও একদিন সম্পূর্ণ বায়ুমণ্ডলে ঢুকিয়া ধংস হইয়া যাইবে।
ভ্যানগার্ড
এই উপগ্রহটিকে আকাশে নিক্ষেপ করা হয় ১৯৫৮ সালের ১৭ মার্চ তারিখে। রকেট বাদে ইহার ওজন মাত্র ৩.৫ পাউণ্ড, আকৃতি বাতাবিলেবুর মতো গোল। কক্ষভ্রমণের সময় ভূপৃষ্ঠ হইতে ইহার দূরত্ব হয় কোনো সময় ৪০০ মাইল এবং কোনো সময় ২৫০০ মাইল। এক্সপ্লোরার উপগ্রহটি যতখানি বায়ুমণ্ডলের ভিতরে আসে, ভ্যানগার্ড ততখানি আসে না, বরং বাহিরেই থাকে বেশি। তাই ইহার গতিবেগ কমিতে এক্সপ্লোরারের চেয়ে সময়ও লাগিবে বেশি। অতঃপর ইহাও ধ্বংস হইবে। তবে আশার কথা এই যে, ভূপৃষ্ঠ হইতে হাজার মাইল উর্ধে কক্ষপথ রচনা করিয়া চিরস্থায়ী উপগ্রহ স্থাপনের চেষ্টা চলিতেছে; হয়তো অচিরেই চেষ্টা সফল হইবে।
.
# কৃত্রিম গ্রহ
লুনিক ১
এই কৃত্রিম গ্রহটি ১৯৫৯ সালের ২ জানুয়ারি তারিখে রাশিয়ার বিজ্ঞানীগণ আকাশে ক্ষেপণ করেন। ইহার ওজন ৩,২৪৫ পাউণ্ড। সূর্য হইতে ইহার গড় দূরত্ব ১০ কোটি ৭৮ লক্ষ মাইল। কিন্তু এই দূরত্ব সব সময় সমান থাকে না। কক্ষপথের বক্রতার দরুন দূরত্ববৃদ্ধি হইয়া কোনো সময় হয় ১২ কোটি ৪৫ লক্ষ মাইল, আবার কমিয়া হয় ৯ কোটি ১১ লক্ষ মাইল। লুনিক সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে ৪৫০ দিনে অর্থাৎ ১৫ মাসে। আমাদের পৃথিবীর বৎসর হইতে লুনিকের বৎসর কিছু বড়। বিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, লুনিক আকাশে থাকিয়া সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকিবে অনন্তকাল। কেননা সে কখনও বায়ুমণ্ডলের আওতায় পড়ে না।
পাইওনিয়ার ৪
১৯৫৯ সালের ৩ মার্চ তারিখে আমেরিকার বিজ্ঞানীগণ এই গ্রহটিকে আকাশে নিক্ষেপ করেন। ইহার ওজন মাত্র ১৩.৪ পাউণ্ড। এই ক্ষুদ্র গ্রহটি ৩৯২ দিনে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। সূর্য হইতে ইহার গড় দূরত্ব ৯ কোটি ৬৬ লক্ষ ৫০ হাজার মাইল। কিন্তু ইহা কমিয়া কোনো সময় হয় ৯ কোটি ২২ লক্ষ মাইল, আবার বৃদ্ধি পাইয়া হয় ১০ কোটি ৬১ লক্ষ মাইল।
লুনিক ১ এবং পাইওনিয়ার ৪ –এই উভয় গ্রহের কক্ষপথ পৃথিবী ও মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথের মাঝখানে অবস্থিত। তবে উহার কোনোও অংশ পৃথিবীর কক্ষপথকে ছেদ করিয়াছে, কিন্তু মঙ্গলের কক্ষপথকে কোথায়ও ছেদ করে নাই। বিজ্ঞানীদের মতে, পাইওনিয়ার ৪ আকাশে থাকিয়া অনন্তকাল সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে থাকিবে।
আলোচ্য গ্রহ ও উপগ্রহদের কাহাকেও দূরবীন ব্যতীত খালি চোখে দেখা সম্ভব নহে।
————
১৫. প্রকৃতি, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পৃ. ৮।
১৬. মহাকাশের ঠিকানা, অমল দাসগুপ্ত, পৃ. ৫৭–৫৯।
১৭. পৃথিবীর ঠিকানা, অমল দাসগুপ্ত, পৃ. ৮৩-৮৪।
১৮. মহাকাশের ঠিকানা, অমল দাসগুপ্ত, পৃ. ২৯।
১৯. মহাকাশের ঠিকানা, অমল দাসগুপ্ত, পৃ. ৫৫-৫৭।
২০. মহাকাশের ঠিকানা, অমল দাসগুপ্ত, পৃ. ১৮৩।
২১. মহাকাশের ঠিকানা, অমল দাসগুপ্ত, পৃ. ১৮১।
২২. সরল বাঙ্গালা অভিধান, সুবলচন্দ্র মিত্র, পৃ. ৪৩২।
২৩. মহাশূন্য থেকে দেখা পৃথিবী, মীর ফখরুল কাইয়ূম (অনুবাদক), পৃ. ৭২।
০৯. বিজ্ঞান মতে সৃষ্টিতত্ত্ব (জীব বিষয়ক)
বিজ্ঞান মতে সৃষ্টিতত্ত্ব
জীব বিষয়ক
জীবন রহস্য জানার কৌতূহলটি মানবমনে বহুদিনের পুরাতন। এই কৌতূহলের নিবৃত্তির জন্য মানুষ বহু মতবাদের জন্ম দিয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে মাত্র দুইটি। উহার একটি হইল সৃষ্টিবাদ, অপরটি বিবর্তনবাদ।
বর্তমান জগতে আমরা যত রকম গাছপালা ও জীব-জানোয়ার দেখিতেছি, ঈশ্বর নামক এক পরম পুরুষ তাহার প্রত্যেকটিকে বর্তমান রূপেই সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীতে ছাড়িয়া দিয়াছেন; ইহাদের মধ্যে কাহারও ‘জাতিগত রূপ’-এ কোনো পরিবর্তন বা নূতনত্ব নাই; ইহারা প্রত্যেকে নিজ নিজ জাতিগত রূপ ও চরিত্রগত বৈশিষ্ট বজায় রাখিয়া বংশবৃদ্ধি করিতেছে মাত্র –সাধারণত এইরূপ ধারণাকে বলা হয় সৃষ্টিবাদ এবং জড় কিংবা জীবজগতে এক-এর রূপান্তরে বহুর উৎপত্তি – এইরূপ ধারণাকে বলা হয় বিবর্তনবাদ।
পূর্বে আলোচিত বেদ ও বাইবেলাদির সৃষ্টিতত্ত্বসমূহ সৃষ্টিবাদের অন্তর্ভুক্ত এবং সামান্য মতানৈক্য থাকিলেও জগতের যাবতীয় ধর্মীয় মতবাদই সৃষ্টিবাদের আওতাভুক্ত। জগত ও জীবনের সৃষ্টি সম্বন্ধে যাবতীয় বিজ্ঞানীদের সর্বস্বীকৃত যে মত, তাহাই বিবর্তনবাদ। এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা পরে করিব।
.
# প্রাণ কি?
প্রাণ কি, এই প্রশ্নের উত্তর এক কথায় দেওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। তাহার কারণ এই যে, প্রাণ মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে।
আমরা প্রাণের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিব না তাহার লক্ষণ ব্যতিরেকে। প্রাণের লক্ষণ প্রধানত স্পন্দন ক্ষমতা, বোধশক্তি, খাদ্যের সাহায্যে দেহপুষ্টি, বংশবৃদ্ধি ইত্যাদি। ইহার মধ্যে, খাদ্যের সাহায্যে দেহপুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি –এই দুইটি প্রধান এবং সৃষ্টির আদিম প্রক্রিয়া।
ধর্মীয় মতে, জীবন জীবদেহ হইতে ভিন্ন। দেহসৃষ্টির পূর্বে উহা কোথায়ও কোনো অবস্থায় বর্তমান ছিল এবং দেহাবসানের পরেও কোনো অবস্থায় কোথায়ও থাকিবে। এই মতে, দেহ পার্থি এবং জীবন ঐশ্বরিক।
জগতের যাবতীয় কার্যাবলীর মধ্যে যে সকল কার্যের কারণসমূহ সাধারণ মানুষের সহজবোধ্য, তাহাকে পার্থিব এবং যে সকল কার্যের কারণসমূহ সহজবোধ্য নহে, তাহাকে ঐশ্বরিক বলাই ধর্মীয় মতবাদের নীতি। বিশেষত যে সকল ঘটনাকে ঐশ্বরিক বলা হয়, তাহার কোনো কারণ খোঁজ করিতে যাওয়াও ধর্মীয় মতে নিষেধ। বরং বলা হয়, উহা গুরুতর অন্যায় বা মহাপাপ। কিন্তু বিজ্ঞানের নীতি হইল অজানাকে জানা ও অচেনাকে চেনা। তাই ধর্মের শত বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও বিজ্ঞানীগণ প্রাণসৃষ্টির রহস্য উদঘাটনের প্রচেষ্টায় বিরত থাকিতে পারেন নাই। বিজ্ঞানীগণ এই প্রচেষ্টায় যেটুকু সাফল্য লাভ করিয়াছেন, এখন তাহার সামান্য আলোচনা করিব।
.
# জৈব পদার্থ
আমরা পূর্বের আলোচনায় জানিয়াছি যে, জগতের যাবতীয় পদার্থ দুই জাতীয় –মৌলিক ও যৌগিক। আবার যে সব পদার্থের দ্বারা উদ্ভিদ ও জীবদেহ তৈয়ারী, তাহাকে বলা হয় জৈব পদার্থ, বাকিগুলিকে বলা হয় অজৈব।
জৈব ও অজৈব পদার্থের মধ্যে আসল পার্থক্য এই যে, জৈব পদার্থের প্রত্যেকটি অণুর কেন্দ্রে সব সময়ই থাকে একটি মৌলিক পদার্থের পরমাণু– কার্বন। কোনো অজৈব পদার্থের অণুর কেন্দ্রে কখনও কার্বন থাকে না। কার্বনকে বাংলা ভাষায় বলা হয় অগার। যে কোনো জৈব পদার্থ পোড়াইলে অঙ্গার পাওয়া যায়। কিন্তু কোনো অজৈব পদার্থ পোড়াইলে কখনও অঙ্গার পাওয়া যায় না। যেমন –কাঁচ, পাথর বা কোনো ধাতু পোড়াইয়া কিছুতেই অঙ্গার পাওয়া যাইবে না। যেহেতু তাহাদের কোনো অণুর কেন্দ্রেই কার্বন বা অঙ্গর নাই।
জৈব পদার্থের মুখ্য উপাদান কার্বন হইলেও তাহার সাথে পদার্থবিশেষে মিশিয়া থাকে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, গন্ধক, ফসফরাস এবং আরও অনেক পদার্থ। জৈব পদার্থের অণুর গর্ভে কার্বনের সঙ্গে ইহাদের বিভিন্ন জাতীয় পরমাণুর বিভিন্ন ভঙ্গিতে মিলনের ফলে জন্ম হয় বিভিন্ন জাতীয় জৈব পদার্থের। যেমন –কার্বন ও হাইড্রোজেন মিলিয়া হয় হাইড্রোকার্বন। আর ইহা হইতে হয় নানাবিধ খনিজ তৈল বা ঐ জাতীয় যাহা কিছু।
জীবদেহের রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা সকলই জৈব পদার্থ; এমনকি কফ, থুথু, ঘর্ম এবং মল-মূত্রও। ইহাদের স্বাভাবিক ক্ষয়ের পূরণ ও পুষ্টির জন্য জীবের আবশ্যক হয় খাদ্যের। খাদ্য গ্রহণের আসল উদ্দেশ্য হইল কার্বন সংগ্রহ করা। জীবের জীবন সংগ্রামে খাদ্য লইয়া যে কাড়াকাড়ি ও মারামারি, তাহা সমস্তই এই কার্বন সংগ্রহের ঝামেলা।
গাছেরা কার্বন সংগ্রহ করে বাতাস হইতে এবং জীব-জন্তুরা কার্বন সংগ্রহ করে শাক-পাতা, তরি-তরকারি ও জীবজন্তুর মাংস হইতে। সংগৃহীত কার্বন জীবদেহে বিবিধ প্রক্রিয়ার শেষে রূপান্তরিত হয় জৈব পদার্থে। আবার বহুকাল মাটির তলায় চাপা থাকিয়া গাছপালা রূপান্তরিত হয় কয়লায় এবং জীবজন্তুর দেহ রূপান্তরিত হয় খনিজ তৈলে।
এতক্ষণ যাহা বলা হইল, তাহা সবই জৈব পদার্থের ব্যবহার ও রূপান্তর বিষয়ক। এখন প্রশ্ন থাকিল এই যে, জৈব পদার্থের সৃষ্টি হইল কিভাবে? বিজ্ঞানীগণ এ প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।
জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ আলোক বিশ্লেষক যন্ত্রের সাহায্যে জানিতে পারিয়াছেন যে, উত্তাপের কম বেশি হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর নক্ষত্র আছে। কোনো শ্রেণীর নক্ষত্রের উত্তাপ ২৮,০০০° সে. পর্যন্ত বা আরও বেশি, আবার কোনো শ্রেণীর নক্ষত্রের উত্তাপ মাত্র ৪,০০০° সে. এবং উহার মধ্যবর্তী উত্তাপে আছে অজস্র নক্ষত্র। স্পেক্টোস্কোপ যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন নক্ষত্রের উপাদান বিশ্লেষণ। দ্বারা বিজ্ঞানীরা জানিতে পারিয়াছেন যে, খুব বেশি উত্তপ্ত নক্ষত্রদের কার্বন পরমাণুরা একা একা ভাসিয়া বেড়ায়, অন্য কোনো পরমাণুর সাথে জোড় বাঁধে না। কিন্তু যে সকল নক্ষত্রের উত্তাপ ১২,০০০° সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি, সেখানে কার্বন পরমাণু হাইড্রোজেন পরমাণুর সঙ্গে জোড় বাঁধিয়া সৃষ্টি করিয়াছে হাইড্রোকার্বন। এই হাইড্রোকার্বন একটি জৈবিক পদার্থ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এইখান হইতেই জৈবিক পদার্থ সৃষ্টির সূত্রপাত।
আমাদের সূর্যের বাহিরের উত্তাপ প্রায় ৬০০০° সে.। সেখানে দেখা যায় যে, কার্বনের সঙ্গে একাধিক মৌলিক পদার্থের পরমাণুর মিলন ঘটিয়াছে। যেমন –কার্বনের সঙ্গে হাইড্রোজেন, কার্বনের সঙ্গে নাইট্রোজেন, এমনকি কার্বনের সঙ্গে কার্বনের। ইহাতে সেখানে একাধিক জৈব পদার্থের জন্ম হইয়াছে।
ভূপতিত উল্কাপিণ্ডের দেহ পরীক্ষা করিয়া বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পাইয়াছেন যে, উল্কার দেহে কার্বন ও ধাতুর মিলনে জন্ম লইয়াছে কার্বাইড। ইহা একটি জৈব পদার্থ।
বিজ্ঞানীরা বলেন যে, নক্ষত্র, সূর্য ও উল্কার দেহে যে প্রক্রিয়ায় জৈব পদার্থ জমিতে পারিয়াছে, পৃথিবীতেও এককালে অনুরূপ প্রক্রিয়ায় জৈব পদার্থসমূহের জন্ম হইয়া থাকিবে। বিজ্ঞানীরা তাহাদের পরীক্ষাগারে কৃত্রিম উপায়ে বহু জৈব পদার্থ তৈয়ার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যথা –শর্করা, প্রোটিন, স্নেহপদার্থ (চর্বি জাতীয়), নীল, ভিটামিন, হর্মোন ইত্যাদি।
বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, প্রোটিন তৈয়ার হয় হাজার হাজার কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও ও নাইট্রোজেন পরমাণুর সুবিন্যস্ত সংযোগে এবং পৃথিবীর আদিম সমুদ্রে প্রোটিন তৈয়ার হইবার মতো অনুকূল অবস্থাও বজায় ছিল। পৃথিবীর আদিম সমুদ্রে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া হাইড্রোকার্বনের নানা রূপান্তরে তৈয়ার হইয়াছিল প্রোটিন এবং তাহা হইতে জন্ম লইয়াছিল। জীবদেহের মূল উপাদান প্রোটোপ্লাজম।
.
# প্রোটোপ্লাজম কি?
প্রকৃতির একমাত্র কাজ — পরিবর্তন বা রূপান্তর। ইহাকে বিবর্তন বলা যায়। বিভিন্ন বিষয়ে প্রাকৃতিক পরিবর্তনে সময়ের ব্যবধান অত্যধিক। প্রকৃতি দুধকে দধি এবং তালের রসকে তাড়ি করিতে কয়েক ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই পারে। কিন্তু রেডিয়ামকে শীশায় পরিণত করিতে তাহার সময়। লাগে লক্ষ লক্ষ বৎসর। ঐরূপ কার্বনাদি জৈব পদার্থ হইতে একটি প্রোটোপ্লাজম তৈয়ার করিতে প্রকৃতির সময় লাগিয়াছে প্রায় একশত কোটি বৎসর।
পদার্থ জৈব বা অজৈব, যাহাই হউক, উহা জীব নামে অভিহিত হইতে পারে না, যে পর্যন্ত উহাতে জীবনের কোনো লক্ষণ প্রকাশ না পায়। পূর্বেই বলিয়াছি যে, জীবনের প্রধান লক্ষণ –দেহপুষ্টি ও বংশবিস্তার। কোনো পদার্থে যদি ঐ দুইটি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়তার সহিত বলা যায় যে, ঐ পদার্থটি সজীব। এখন দেখা যাক যে, কোন পদার্থে ঐ লক্ষণ। দুইটি পাওয়া যায়।
প্রোটোপ্লাজমের মুখ্য উপাদান প্রোটিন এবং ইহা ভিন্ন আরও জৈব-অজৈব অনেকগুলি পদার্থ। উহা আদিম সমুদ্রে জলে গোলা দ্রব অবস্থায় ছিল। উহাকে ইংরাজিতে বলে সলিউশন। চিনি বা লবণ গোলা জলকেও সলিউশন বলা যায়। কিন্তু প্রোটোপ্লাজম ঐ ধরণের সলিউশন নহে, উহা এক বিশেষ ধরণের সলিউশন। ইংরাজিতে বলা হয় কলয়ডাল সলিউশন।
চিনি বা লবণ জলে দ্রবীভূত হইলে উহাকে ছাকন প্রণালী দ্বারা জল হইতে ভিন্ন করা যায় না। কিন্তু কলয়ডাল সলিউশন ছাঁকুনিতে আটকা পড়ে। তাই বলিয়া এই আটকা পড়াই ইহার বিশেষত্ব নহে। মাটি বা চুন গোলা জলও সূক্ষ্ম ছাঁকুনি দ্বারা ছাকিলে মাটি ও চুন ভিন্ন হইয়া যায়। কিন্তু ইহা কলয়ডাল সলিউশন নহে। যেহেতু মাটি বা চুন জলে গোলা হইলে সময়ান্তরে উহা থিতাইয়া পড়ে। কিন্তু কলয়ডাল সলিউশন কোনো কালেই থিতায় না। উহা এইরূপ এক বিশেষ পদার্থ যে, জলে সম্পূর্ণ মেশে না, অথচ কোনোকালেই থিতায় না। জানিয়া রাখা উচিত যে, কলয়ডাল সলিউশন জৈব পদার্থের হইতে পারে, আবার অজৈব পদার্থেরও হইতে পারে। অজৈব পদার্থের কলয়ডাল সলিউশন হয়তো জলে সম্পূর্ণ মিশিয়া থাকে, নচেৎ থিতাইয়া পড়ে। কিন্তু জৈব পদার্থের কলয়ডাল সলিউশনই জলে সম্পূর্ণ মেশে না, অথচ থিতাইয়া পড়ে না। এইখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অজৈব পদার্থের সঙ্গে জৈব পদার্থের একটি চরিত্রগত পার্থক্য প্রকট হইয়া উঠিয়াছে এবং সে এখন হইতে আর জড় পদার্থের নিয়মে অপরের শক্তিতে চালিত হইতে রাজি নহে। তাই কলয়ডাল সলিউশনের এই স্বকীয়তা।
কলয়ডাল সলিউশনের আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, জলে অন্য যে সব জৈব-অজৈব পদার্থ থাকে, উহাকে আত্মসাৎ করিয়া নিজ দেহ পুষ্ট করিতে থাকে। এইভাবে লক্ষ লক্ষ বৎসর অতিবাহিত হইলে কলয়ডাল জৈব পদার্থটি আয়তনে ও ওজনে বহুগুণ বৃদ্ধি পায় ও শেষে ফাটিয়া দুই টুকরা হইয়া যায়। কিন্তু দুই টুকরা হইয়া উহারা মরে না, আলাদা আলাদা থাকিয়া আগের মতোই পুষ্ট হইতে থাকে এবং কালক্রমে আবার দুই টুকরা ফাটিয়া চারি টুকরা হয় ও কালে চারি টুকরা ফাটিয়া আট টুকরা হয়। এইভাবে চলিতে থাকে কলয়ডাল পদার্থটির পুষ্টি ও বংশবৃদ্ধির ধারা। এইখানে লক্ষ্যণীয় এই যে, কলয়ডাল পদার্থটির মধ্যে জীবন-এর সর্বাপেক্ষা বড় দুইটি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে– একটি পুষ্টি, আর একটি বংশবিস্তার। এই বিশেষ ধরণের কলয়ডাল পদার্থটির নাম প্রোটোপ্লাজম বা সেল (Cell), বাংলায় বলা হয় জীবকোষ।[২৪]
বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, আদিম সমুদ্রের জলে অতি তুচ্ছ প্রোটোপ্লাজম বিন্দুকে আশ্রয় করিয়াই হইয়াছিল প্রাণ-এর অভ্যুদয় এবং জগতে জীবন-এর অভিযান শুরু।
.
# কৃত্রিম উপায়ে প্রাণসৃষ্টি
প্রকৃতিরাজ্যে আদিম প্রাণসৃষ্টি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক মতবাদের যে আলোচনা করা হইল তাহাতে বুঝা যায় যে, ‘প্রাণ’ শক্তিটি কোনো কোনো পদার্থের সম্মিলিত রাসায়নিক ক্রিয়ায় উদ্ভূত একটি অভিনব শক্তি। এইখানে একটি প্রশ্ন আসিয়া থাকে যে, প্রকৃতিরাজ্যে রাসায়নিক সম্মিলনে এখনও কি প্রাণের সৃষ্টি হইয়া থাকে? ইহার উত্তরে বিজ্ঞানীগণ বলিয়া থাকেন– না। কেননা, তখনকার পৃথিবীর প্রাকৃতিক অবস্থা এমন এক পর্যায়ে ছিল অর্থাৎ তাপ, আলো, বায়ুচাপ, জলবায়ুর উপাদান ইত্যাদির পরিমাণ এরূপ ছিল, যাহাতে তখন প্রাণের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু সেই আদিম অবস্থা এখন আর নাই এবং ভবিষ্যতেও তাহার পুনরোদ্ভব হইবার সম্ভাবনা নাই। এখন চলিতেছে বীজোৎপন্ন প্রাণপ্রবাহ অর্থাৎ প্রাণ হইতে প্রাণের উদ্ভবের ধারা। তবুও অনেকদিন হইতে বিজ্ঞানীগণ ভাবিতেছিলেন যে, কৃত্রিম উপায়ে অবস্থান্তর ঘটাইয়া প্রাণ সৃষ্টি করা যায় কি না?
কৃত্রিম উপায়ে প্রাণসৃষ্টি ও চন্দ্রলোকে গমন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব কি না, তাহা লইয়া আলোচনা হইয়াছিল কয়েক বৎসর পূর্বে বিজ্ঞানীদের এক সম্মেলনে এবং আলোচনায় স্থির হইয়াছিল যে, উহা সম্ভব। অতঃপর অনেক বিজ্ঞানী গবেষণা চালাইতে থাকেন উহা বাস্তবায়নের জন্য। বিষয় দুইটির লক্ষ্যবস্তু হইল পরস্পর বিপরীতমুখী। উহার একটি হইল বহির্জগতে সুদূর মহাকাশে অবস্থিত এবং অপরটি হইল জীবের অন্তর্জগতে, একেবারে কেন্দ্রে অবস্থিত। এই বিষয় দুইটি লইয়া দুই দল বৈজ্ঞানিকের মধ্যে চলিতে থাকিল অতিদূর ও অতিনিকটের রহস্যোদঘাটনের পাল্লা।
যাঁহাদের গবেষণার পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণাদি বহির্মুখী অর্থাৎ আকাশ-মহাকাশ জুড়িয়া যাহাদের কর্মক্ষেত্র, তাহাদের গবেষণার যাবতীয় সংবাদ দৈনিক, মাসিক ও বেতারাদিতে ব্যাপক প্রচারের ফলে পৃথিবীময় তুমুল হৈ চৈ পড়িয়া গিয়াছিল অনেক বারেই। কোনো মানুষের কাছে এখন আর উহা অজানা আছে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষত টেলিভিশন যন্ত্রযোগে চন্দ্রাভিযানের দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিয়াছেন হাজার হাজার লোকে। পক্ষান্তরে, যাহারা প্রাণসৃষ্টি সম্বন্ধে গবেষণা করিতে থাকেন, তাহাদের গবেষণার পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণাদি হইল অন্তর্মুখী, অর্থাৎ গবেষণাগারেই সীমাবদ্ধ এবং জনসাধারণের দৃষ্টিসীমার আড়ালে অবস্থিত। বিশেষত চন্দ্রাভিযানের সংবাদের ন্যায় প্রাণসৃষ্টির সংবাদ তত ব্যাপক আকারে প্রচারিত হয় নাই। তাই কৃত্রিম উপায়ে প্রাণসৃষ্টি’ –এই বিষয়টি অনেকেই অবগত নহেন। কিন্তু প্রাণ সৃষ্টির অভিযান সফল হইয়াছে চন্দ্রাভিযান সফল হইবার প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে।
১৯৬৭-৬৮ সালের শীতকালে (ডিসেম্বর-জানুয়ারি) ক্যালিফোর্নিয়ার। স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ডক্টর আর্থার কোর্ণবার্গ এবং তাহার সহকারীগণ মিলিয়া টেস্টটিউবে অজৈব পদার্থ C, H, ০, N ইত্যাদির সংমিশ্রণে জৈব ভাইরাস সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন। উক্ত ভাইরাস প্রকৃতিজাত (আল্লাহর সৃষ্টি) জীবন্ত ভাইরাসের ন্যায় নড়াচড়া করে। ইহাতে বহুকালের বৈজ্ঞানিক কল্পনা বাস্তবে পরিণত হয়। [ লাইফ ইন এ টেস্টটিউব, দি এ্যামেজিং ওয়ার্লড অফ নেচার, ডোনাল্ড, পৃ. ২৩০]
আলোচ্য আবিষ্কারটি হইল বিজ্ঞানীদের প্রযোজিত জীবননাট্য অভিনয়ের মাত্র প্রথম অক। ইতঃপূর্বে ১৮২৮ খ্রী. জার্মান বৈজ্ঞানিক ফ্রেড্রিক ওহলার টেস্টটিউবে ইউরিয়া (একটি জৈব পদার্থ) তৈয়ার করিয়া প্রমাণ করিয়া দেন, প্রকৃতির ন্যায় মানুষ জৈব পদার্থ তৈয়ার করিতে পারে। জানি না, ইহার যবনিকা কত দূরে। সে যাহা হউক, এখন অভিজাত প্রাণের বিবর্তন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।
.
# প্রাণের বিবর্তন
প্রাক-ক্যাম্ব্রিয়ান যুগের শেষের দিকের কথা। তখন আকৃতি ও প্রকৃতিতে সেল বা জীবকোষগুলি জীব পদবাচ্য নহে। কিন্তু উহাতে জীবনের প্রধান দুইটি লক্ষণ যখন প্রকাশ পাইয়াছে, তখন উহাকে আর নির্জীবও বলা চলে না। জীবকোষগুলির কোনো ইন্দ্রিয় নাই, বিশিষ্ট কোনো চেহারা নাই, আহার করে সর্বশরীর দিয়া চুষিয়া। পর্যাপ্ত পুষ্টিকর আহার পাইলে অতিদ্রুত বংশবৃদ্ধি করিতে পারে। শরীরের কোনো এক স্থানে আঘাত পাইলে সর্বশরীর শিহরিয়া উঠে। ইহাতে দেখা যায় যে, জীবকোষে জীবনের আর একটি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে– বোধশক্তি।
আদিম জীবকোষের বংশাবলী আজও দেখা যায় খাল-বিলের নোংরা জলে। উহা নরম তুলতুলে জেলির মতো শেওলা জাতীয় এক প্রকার জলো পদার্থ। অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখিলে উহাতে দেখা যায় অসংখ্য বিন্দু বিন্দু জীবকোষ। ইহাদের বলা হয় অ্যামিবা। ইহারাই জীবজগতের আদিম প্রাণী এবং এককোষবিশিষ্ট জীব।
কালক্রমে কোনো কোনো জীবকোষ একা একা না থাকিয়া মধুপোকার মতো কতগুলিতে একত্র জটলা করিয়া থাকিতে আরম্ভ করে। জটলার বাহিরের দিকের কোষগুলি খাদ্য সংগ্রহ করিলে ভিতরের কোষগুলি উহা চুষিয়া লয় এবং স্বস্থানে থাকিয়া উহাদের পুষ্টি ও বংশবৃদ্ধি হইতে থাকে। ইহার ফলে জটলাটির কলেবর বৃদ্ধি পায়। জটলার ভিতরের কোষগুলির স্বতন্ত্র সত্তা বজায় থাকে, কিন্তু বাহিরে হইয়া যায় এক। এইভাবে নানা আকৃতিবিশিষ্ট জটলা তৈয়ার হইয়া সমুদ্রজলে হয় বহুকোষী জীব-এর আবির্ভাব।
উদ্ভিদ ও জীব
আজ হইতে প্রায় একশত কোটি বৎসর আগের কথা। তখন ভূপৃষ্ঠের কোথায়ও গাছপালা বা জীবজন্তুর চিহ্ন নাই। সমুদ্রের জল লবণহীন, কিছুটা গরম এবং উহাতে মিশিয়া আছে নানাবিধ জৈবাজৈব পদার্থ, অধিকাংশই কার্বন-ডাই-অক্সাইড। আকাশ ঘন কুয়াশায় ভরা, যেহেতু তখনও আকাশের সমস্ত জলীয় বাষ্প বৃষ্টির আকারে ঝরিয়া পড়ে নাই। কাজেই ভূপৃষ্ঠের কোথায়ও অবাধে সূর্যের আলো পৌঁছে না। বাতাসে অক্সিজেন নাই বলিলেই চলে, আছে প্রচুর কার্বন-ডাই অক্সাইড। এহেন অবস্থার মধ্যে সমুদ্রের জলে অতি ধীরে ধীরে চলিতেছিল জীবাণুদের বংশবিস্তার।
কালক্রমে পৃথিবী আরও শীতল হইয়া আকাশের সমস্ত জলীয় বাষ্প প্রায় নিঃশেষে ঝরিয়া পড়িলে, সূর্যালোক অবাধে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে থাকে এবং সূর্যালোক পাইয়া জীবাণুরাজ্যে এক নবজাগরণের সাড়া পড়িয়া যায়।
শীতের দিনে ভোরের রৌদ্র সকলেই ভালোবাসে। কিন্তু উহা উপভোগ করিবার সুযোগ সকলে। পায় না। আবার রোদ পোহাইলে আরাম পাওয়া যায় বটে, কিন্তু উহাতে পেট ভরে না। রোদ পোহাইলে যদি পেট ভরিত, তাহা হইলে খাদ্য সংগ্রহের ঝঞ্ঝাট না করিয়া জীবেরা আজীবন রোদ পোহাইত। সাগরের জলে রৌদ্র পড়িলে যে সকল জীবাণু উহা উপভোগ করিবার সুযোগ পাইল, তাহারা একটি আশ্চর্য সুবিধা পাইয়া গেল। উহারা দেখিল যে, রোদ পোহাইলে পেট ভরে। সুতরাং উহারা নড়াচড়া না করিয়া সংবৎসর শুধু রোদ পোহাইয়া দেহ পুষ্ট ও বংশবৃদ্ধি করিতে লাগিল। এইরূপ সুবিধাভোগী জীবাণুরা হইল উদ্ভিদ। আর যে সকল জীবাণু সমুদ্রের গভীর জলে থাকিবার দরুন বা অন্য কোনো কারণে সূর্যালোকের সংস্পর্শ পাইল না, খাবার সংগ্রহের জন্য তাহাদের কিছু কিছু নড়াচড়া না করিয়া গত্যন্তর রহিল না। সূর্যদেবের শাপ এই সকল জীবাণুর বর হইল। অসুবিধাভোগী জীবাণুরা হইল জীব বা জন্তু। এই বিষয়টি আর একটু বিস্তারিতভাবে বলি।
আজকাল আমরা গাছপালার পাতায় যে সবুজ রঙের বাহার দেখি, উহা রঙের বাহার মাত্র নহে। গাছের পাতায় সূর্যালোক পতিত হইয়া সবুজ রঙের একটি প্রলেপ পড়ে। উহাকে বলে ক্লোরোফিল। ক্লোরোফিল পদার্থটির একটি বিশেষ ক্ষমতা এই যে, উহা বাতাসের কার্বন-ডাই অক্সাইডকে ধরিয়া উহার কার্বন ও অক্সিজেনকে দুই ভাগে বিভক্ত করে এবং কার্বনকে গাছের দেহপুষ্টির জন্য রাখিয়া অক্সিজেনকে বাতাসে ফিরাইয়া দেয়। যে সকল জীবাণুর দেহে সূর্যালোক পতিত হইল, তাহাদের শরীরে জন্সিল ক্লোরোফিল এবং উহার সাহায্যে জীবাণুরা বসিয়া বসিয়া খাবার খাইয়া অচল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইল। ইহারা জাতিতে হইল উদ্ভিদ। পূর্বেই বলিয়াছি যে, ঐ সময়ের বাতাসে ছিল প্রচুর পরিমাণে কার্বন-ডাই-অক্সাইড। তাই উদ্ভিদাণুরা অনায়াসে অতিমাত্রায় পুষ্টিকর খাদ্য কার্বন পাইয়া দ্রুত বংশবৃদ্ধি করিতে থাকে এবং বিবর্তনের ধারা অনুসারে নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া ক্রমোন্নতির পথে আগাইয়া চলে। বিবর্তনের প্রথম ধাপে দেখা যায় শেওলা জাতীয় বিবিধ নিম্নশ্রেণীর জলজ উদ্ভিদ।
যে সকল জীবাণু সূর্যালোক হইতে বঞ্চিত রহিল, তাহারা অন্য উপায়ে কার্বন সংগ্রহের চেষ্টায়। থাকিল। উদ্ভিদাণুর দেহে প্রচুর কার্বন মজুত পাইয়া জীবাণুরা উহাদের আত্মসাৎ করিতে লাগিল। তৈয়ারী খাবার সবসময় মুখের কাছে থাকে না, উহা খোঁজ করিতে হয় এবং যদিও দুই-একটি মুখের কাছে ভাসিয়া আসে, তবুও উহাকে খাইয়া ফেলিলে কিছুদূর না আগাইয়া আর একটি পাওয়া অসম্ভব। তাই জীবাণুরা খাবার সংগ্রহের তাগিদেই কিছু কিছু চলাফেরায় অভ্যস্ত হইল। বিশেষত উদ্ভিদাণুদের খাইয়া খাইয়া জীবাণুদের রাক্ষুসেপনা বাড়িয়া গেল। সবল জীবাণুরা দুর্বল জীবাণুদের খাইতে আরম্ভ করিল। ইহাতে আর একটি ফল হইল এই যে, শিকারী চায় ধরিতে আর শিকার চায় পালাইতে, কাজেই আক্রমণ ও আত্মরক্ষার জন্য জীবাণুরা দ্রুত চলাচলে অভ্যস্ত হইল এবং প্রচুর আয়াসলভ্য খাদ্য খাইয়া বিবর্তনের ধারামতে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া ক্রমোন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহাদের বিবর্তনের প্রথম ধাপে দেখা যায় ট্রাইলোবাইট নামক কয়েক শ্রেণীর পোকা জাতীয় জলজ জীব।
বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, মানুষ, পশু, পাখি ইত্যাদি জীব ও বৃক্ষ, লতা, তৃণাদি উদ্ভিদ –ইহারা সকলেই এককালে ছিল সাগরের জলের বাসিন্দা। উহাদের আকৃতি, প্রকৃতি, খাদ্য ও বাসস্থানের যত বৈচিত্র, তাহা ঘটিয়াছে ক্রমবিবর্তনের ফলে।
.
# জীবজগতের বিবর্তন
পরিবর্তন জগতের রীতি। বিশ্বে এমন কোনো পদার্থ নাই, যাহার কোনোরূপ পরিবর্তন বা। রূপান্তর নাই। বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, পৃথিবীতে আজ আমরা যে আম, জাম, শাল, সেগুন। ইত্যাদি বৃক্ষরাজি ও অসংখ্য রকম লতাগুল্ম দেখিতেছি, উহারা চিরকালই ঐরূপ ছিল না। আদিতে উহারা ছিল শেওলা জাতীয় এক প্রকার জলজ উদ্ভিদ এবং হাতি, ঘোড়া, শিয়াল, কুকুর। ও অন্যান্য যাবতীয় জীব, এমনকি মানুষও তাহার বর্তমান রূপে ছিল না। গোড়ার দিকে উহারা সকলেই ছিল এক জাতীয় জলজ পোকা।
প্রকৃতির অমোঘ বিধানে জীবজগতে যে রূপান্তর ঘটিয়া থাকে, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় তাহাকে বলে বিবর্তন (Evolution)। বিবর্তন দুই রকম। যথা –১. মানুষের ইচ্ছা বা বুদ্ধির দ্বারা জন্তু। বা উদ্ভিদের মধ্যে মিলন ঘটাইলে, তাহার ফলে এক ঈপ্সিত স্বতন্ত্র জাতির উৎপত্তি হয় –ইহাকে বলা হয় কৃত্রিম নির্বাচন (Artificial Selection), ২. ইচ্ছা বা বিচারবুদ্ধির বালাই নাই, স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন প্রাণীর মিলন সংঘটন ও নব নব জাতির বিকাশ হইয়া থাকে– ইহাকে বলা হয় প্রাকৃতিক নির্বাচন (Natural selection)। প্রাকৃতিক নির্বাচন ও কৃত্রিম নির্বাচনে পার্থক্য অনেক আছে। প্রধানত কৃত্রিম নির্বাচন বেশি সময়সাপেক্ষ নহে। কিন্তু প্রাকৃতিক নির্বাচনে কোনো প্রাণীর এতটুকু রূপান্তর ঘটিতে সময় লাগে লক্ষ লক্ষ বৎসর।
মেণ্ডেলপন্থী বিজ্ঞানীগণ জীববিজ্ঞানে বিশেষত চিকিৎসা ও উদ্ভিদবিজ্ঞানে তথা কৃষিক্ষেত্রে নানাবিধ অলৌকিক কার্য সম্পাদন করিতেছেন। আমেরিকার স্বনামখ্যাত লুথার মানুষের চাহিদা বা পরিকল্পনানুযায়ী অল্প সময়ের মধ্যে নানারকম নুতন জাতীয় ফুল, ফল বা ফসলের গাছ উৎপন্ন করিয়া দিয়া উদ্ভিদজগতে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। আর প্রাকৃতিক নির্বাচনে বানরের লেজ খসিতে, মস্তিষ্ক বড় হইতে এবং সামান্য কিছু কিছু অবয়বগত পরিবর্তন হইতে সময় লাগিয়াছে সাত কোটি বৎসর।
বিবর্তন কেন হয় এবং কি রকম হয়, এই সকলের বিশদ আলোচনা করা এই ক্ষুদ্র পুস্তকে অসম্ভব এবং যাবতীয় জীবের বিবর্তনের বিষয় আলোচনা করাও সম্ভব নহে। আমরা শুধু মানুষ জাতির বিবর্তনের মাত্র প্রধান প্রধান ধাপগুলির আলোচনা করিব।
বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, জন্মের সময় পৃথিবীর তাপ সূর্যের বহিরাবরণের তাপের সমান ছিল। অতঃপর তাহা বিকীর্ণ হইয়া জীবসৃষ্টির অনুকূল তাপের সৃষ্টি হইতে সময় লাগিয়াছে প্রায় ২০০ কোটি বৎসর। ইহার পর প্রায় ১৫০ কোটি বৎসর হইল পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাব ঘটিয়াছে এবং চোখের দেখায় চিনিতে পারার মতো জীবের সৃষ্টি হইয়াছে মাত্র ৫০ কোটি বৎসরের মধ্যে। কিন্তু উহার মধ্যে ৫ হাজার বৎসরের বেশি সময়ের লিখিত ইতিহাস মানুষের হাতে নাই।
এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, অনন্ত অতীতের বহু খবর মানুষ জানিতে পাইয়াছেন ধর্মগুরুদের কাছে এবং ধর্মগুরুরা পাইয়াছেন প্রত্যাদেশরূপে বা সৃষ্টিকর্তার সাথে আলাপ-আলোচনা করিয়া; বিজ্ঞানীগণ উহা পাইলেন কোথায়?
এই কথা সত্য যে, বিজ্ঞানীগণ কোনোরূপ প্রত্যাদেশ বা সৃষ্টিকর্তার দেখা-সাক্ষাত পান নাই। তাঁহারা বলেন যে, সৃষ্টির ইতিহাস লেখা আছে সৃষ্ট পদার্থের গর্ভে। তাহারা যে লিপির সাহায্যে অতীতকালের জীবেতিহাস জানিতেছেন, তাহার নাম জীবাশ্ম বা ফসিল (Fossil)।
.
# ফসিল কি?
ভূতত্ত্ব হইতে জানা যায় যে, পৃথিবীর সমতল ভূমি ও সমুদ্রতল স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে। পর্বতাদি হইতে নদীর জল পলি আনিয়া প্রতি বৎসর সমতলভূমি বা সমুদ্রতলে উহা বিছাইয়া দেওয়ার ফলে ঐ স্তরের সৃষ্টি হয়। ক্রমশ স্তর যতই উঁচু হইতে থাকে, ইহাতে নিম্নাঞ্চলের মাটি কঠিন হইয়া পাথরের আকৃতি ধারণ করে। ভূবিজ্ঞানীগণ বিভিন্ন স্তরের প্রকৃতি ও গুণাগুণ পরীক্ষা করিয়া বলিতে পারেন যে, কোন্ স্তরের বয়স কত।
গাছের গুঁড়ি বহুকাল মাটির নিচে চাপা পড়িয়া থাকিলে উহা পাথরের আকার ধারণ করে। এই অবস্থায় উহাকে আমরা পাথর কয়লা বলি। ঐরূপ কোনো জন্তুর দেহ বহুকাল মাটির নিচে চাপা পড়িয়া থাকিলে উহার কতকালসমূহ পাথরের আকার ধারণ করে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় উহাকে বলা হয় জীবাশ্ম বা ফসিল। সেই স্তর সৃষ্টি হইবার সমকালে ভূপৃষ্ঠে যে জীব বর্তমান ছিল, সেই জীবের দেহের কিছু না কিছু চিহ্ন সেই স্তরে থাকিয়া গিয়াছে এবং উহা ফসিলরূপে বর্তমান আছে। বলা বাহুল্য যে, ভূগর্ভস্থ যে স্তর যত নিমে, সেই স্তর তত পুরাতন এবং যে স্তর যত উপরে, সেই স্তর তত আধুনিক। ভূগর্ভস্থ কোনো বিশেষ স্তরে প্রাপ্ত ফসিল পর্যবেক্ষণ করিয়া বিজ্ঞানীগণ বলিতে পারেন যে, ঐ জন্তুটি কোন যুগে বা কত বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিল এবং উহার আকৃতি, প্রকৃতি, চাল-চলন এমনকি আহার-বিহার কি রকম ছিল।
.
# যুগ বিভাগ
হিন্দুশাস্ত্র মতে, যুগ চারিটি। যথা –সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি.। বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়ায় রবিবারে সত্য যুগের উৎপত্তি হয়। এই যুগের পরিমাণ ১৭,২৮,০০০ বৎসর। এই যুগে মৎস্য, কুর্ম, বরাহ ও নৃসিংহ– এই চারি অবতার। সত্যযুগে বৈবস্বত, মনু, ইক্ষাকু, বলি, পৃথু, মান্ধাতা, পুরোরবা প্রভৃতি রাজা ছিলেন। মানবগণের লক্ষ বৎসর পরমায়ু ও একবিংশতি হস্ত পরিমিত দেহ ছিল।
কার্তিক মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে সোমবারে ত্রেতা যুগের উৎপত্তি। এই যুগের পরিমাণ ১২,৯৬,০০০ বৎসর। ত্রেতায় বামন, পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্র –এই তিন অবতার। এই যুগে। ককুস্থ, ত্রিশঙ্কু, হরিশচন্দ্র, মরুত্ত, অনরণ্য, সগর, অংশুমান, রঘু, অজ, দশরথ প্রভৃতি রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই সময় লোকের পরমায়ু ছিল দশ সহস্র বৎসর এবং দেহ ছিল চতুর্দশ হস্ত পরিমিত।
ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে বৃহস্পতিবারে দ্বাপর যুগের আরম্ভ হয়। এই যুগের পরিমাণ ৮,৬৪,০০০ বৎসর। এই যুগে বলরাম ও বুদ্ধ –এই দুই অবতার। শাল, বিরাট, ময়ূরজ, শান্তনু, দুর্যোধন, যুধিষ্ঠির, জরাসন্ধ প্রভৃতি এই যুগের রাজা ছিলেন। এই কালে মানুষের সহস্র বৎসর পরমায়ু ও সপ্ত হস্ত পরিমিত দেহ ছিল।
মাঘী পূর্ণিমায় শুক্রবারে কলিযুগের উৎপত্তি হয়। এই যুগের পরিমাণ ৪,৩২,০০০ বৎসর। এই যুগের শেষভাগে কল্কি অবতার আবির্ভূত হইবেন। এই সময়ে মানুষের পরমায়ু ১২০ বৎসর এবং দেহ সার্ধ-ত্রিহস্ত পরিমিত। এই যুগের মাত্র ৫,০৭০ বৎসর গত হইয়াছে (বাংলা ১৩৭৭ সন পর্যন্ত)।
উল্লিখিত চারি যুগের শাস্ত্রীয় বিবরণের সমালোচনা বা সত্যাসত্য যাচাই করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে, উহা যুগমানবের কর্তব্য। আলোচ্য যুগচতুষ্টয়ের মোট বয়স ৪৩,২০,০০০ বৎসর এবং কলিযুগের শেষ হইতে এখনও ৪,২৬,৯৩২ বৎসর বাকি। সুতরাং অতীত হইয়াছে ৩৮,৯৩,০৬৮ বৎসর। কলিযুগের অবসানে কোন্ যুগ আসিবে এবং সত্যযুগের পূর্বে কোনোও জীব বা যুগ ছিল কিনা, শাস্ত্রকার তাহার কোনো ইঙ্গিত দেন নাই। আলোচ্য যুগচতুষ্টয়ের অতীত কাল বিজ্ঞানীদের সর্বাধুনিক প্লিটোসেন উপযুগটির সমানও নহে (এই যুগটির বর্তমান বয়স প্রায় ৫০ লক্ষ বৎসর)। পক্ষান্তরে বাইবেলের মতে, বিশ্বের সৃষ্টি বা মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে খ্রী. পূ. ৪০০৪ সালে। অর্থাৎ এখন (১৯৭০) হইতে ৫,৯৭৪ বৎসর আগে।
উপরোক্ত যুগচতুষ্টয়ের বয়সের হিসাবে দেখা যায় যে, মোট বয়সের ১০ ভাগের ৪ ভাগ সত্য যুগ, ৩ ভাগ ত্রেতা যুগ, ২ ভাগ দ্বাপর যুগ এবং ১ ভাগ কলির ভাগে পড়িয়াছে। অর্থাৎ কলির বয়সের দ্বিগুণ দ্বাপর, তিন গুণ ত্রেতা, এবং চারি গুণ পড়িয়াছে সত্য যুগের ভাগে। এইরূপ আঙ্কিক যুগবিভাগ বিজ্ঞানীগণ করেন না, তাঁহাদের যুগবিভাগ অন্য রকম।
প্রত্নতত্ত্ববিদগণ ভূগর্ভের স্তরগুলিকে কালক্রমিক কতগুলি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। উহার এক একটি ভাগকে বলা হয় এক একটি যুগ। এখন হইতে পঞ্চাশ কোটি বৎসর আগের সমস্ত যুগকে একত্রে বলা হয় আর্কেও জোইক (Archaeo Zoic) মহাযুগ বা প্রাক-ক্যামব্রিয়ান যুগ। এই যুগে যে সমস্ত প্রাণী বর্তমান ছিল, তাহাদের অস্তিত্বের সন্ধানটুকু পাওয়া যায় মাত্র, বিশেষভাবে কিছু। জানার উপায় নাই। যেহেতু তাহাদের দেহ ছিল নরম তুলতুলে, দেহে আবরণ বলিতে কিছু ছিল না। তাই তাহাদের কোনো ফসিল ভূগর্ভে পাওয়া যায় না।
ক্যামব্রিয়ান যুগ আরম্ভ হইবার পর হইতে কোনো কোনো প্রাণীদেহ কঠিন খোলস বা বর্মে আবৃত হয়। যেমন– চিংড়ি, কাঁকড়া ইত্যাদি। এই সময় হইতেই শিলালিপি বা ফসিল প্রাপ্ত হওয়া যায়। জীববিজ্ঞানীগণ যে সময় হইতে ফসিল বা শিলালিপির সাহায্যে জীবজগতের ইতিহাস জানিতে পারেন, সেই সময়টিকে তাঁহারা বলেন ঐতিহাসিক যুগ। এই ঐতিহাসিক যুগটিকে আবার তিন পর্যায়ে ভাগ করা হইয়াছে। যথা –পুরাজীবীয় (Palaeo Zoic), মধ্যজীবীয় (Meso Zoic) ও নবজীবীয় (Caino Zoic) যুগ। এই তিনটি যুগের ব্যাপ্তি ৫০ কোটি বৎসর। ইহার মধ্যে পুরাজীবীয় যুগ ৩১ কোটি বৎসর। ইহা ৫০ কোটি বৎসর আগে আরম্ভ হইয়া শেষ হইয়াছে ১৯ কোটি বৎসর আগে। এই যুগটির ৬টি উপযুগ আছে। মধ্যজীবীয় যুগটির ব্যাপ্তি ১২ কোটি বৎসর। ইহা ১৯ কোটি বৎসর আগে আরম্ভ হইয়া শেষ হইয়াছে ৭ কোটি বৎসর আগে। এই যুগটির তিনটি উপযুগ আছে। নবজীবীয় যুগ অর্থাৎ বর্তমান যুগটি মাত্র ৭ কোটি বৎসর আগে আরম্ভ হইয়া এখনও চলিতেছে। ইহার ৫টি উপযুগ আছে। সর্বশেষ উপযুগটির নাম প্লিসটোসেন উপযুগ। এই যুগটি ৫০ লক্ষ বৎসর আগে আরম্ভ হইয়া এখনও চলিতেছে। জীবজগতের বিবর্তন বিশেষত মানুষ জাতির বিবর্তনের ক্ষেত্রে এই প্লিসটোসেন উপযুগটির গুরুত্ব অপরিসীম। বিবর্তনের ক্রমিক ধারা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে যুগ ও উপযুগগুলি সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা থাকা আবশ্যক। এইখানে স্তরক্ৰমিক যুগের একটি তালিকা দেওয়া হইল। উহা পাঠকের বিবর্তনবাদ বুঝিবার সহায়তা করিবে।
স্তরক্রমিক যুগবিভাগ (সাম্প্রতিক হইতে অতীতে)
ক. পুরাজীবীয় যুগ (Palaeo Zoic) এই যুগের প্রথমে ভূপৃষ্ঠে যে স্তরের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা পর্যবেক্ষণ করিয়া বিজ্ঞানীগণ স্থলভাগে কোনো জীবের অস্তিত্ব পান নাই, সমুদ্রে পাইয়াছেন জলজ উদ্ভিদ ও আলপিনের মাথার মতো ক্ষুদ্র এক জাতীয় পোকা, উহাদের বলা হয় ট্রাইলোবাইট। কয়েক কোটি বৎসর পর দেখা যায় যে, ঐ পোকার আকার হইয়াছে প্রায় এক ফুট। বর্তমানে উহার সকল শাখাই বাঁচিয়া নাই। যে দুই একটি দল বাঁচিয়া আছে, খুব সম্ভব তাহারা উহাদের বংশধর কাঁকড়া, গলদা চিংড়ি ইত্যাদি।
ট্রাইলোবাইটদের এক দল নদী বা হ্রদে আশ্রয় লয়। ইহাদের নাম ইউরীপটেরিড়। ভূপৃষ্ঠের আলোড়নে নদী বা হ্রদ শুকাইয়া গেলে উহাদের বেশির ভাগই মারা পড়ে, কৃতক সমুদ্রে চলিয়া যায় এবং কোনো কোনো দল শুকনায়ও বাঁচিয়া থাকে। ইহাদের পরিবর্তিত রূপ বৃশ্চিক, মাকড়সা ইত্যাদি এবং কেহ কেহ উড়িবার ক্ষমতা লাভ করিয়া হয় পতঙ্গ। যাহারা সমুদ্রে চলিয়া যায়, কয়েক কোটি বৎসরের মধ্যে তাহাদের দেহ হয় খোলস বা চর্মে আবৃত (বর্ম নহে)।
বর্মধারী জীব যথা –কাকড়া, কাছিম, শামুকাদি জীবেরা যত সহজে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারে, চর্মধারী জীবেরা তত সহজে আত্মরক্ষা করিতে পারে না। তাই আত্মরক্ষার তাগিদে দ্রুত চলাচলের জন্য চমধারী জীবের দেহে তৈয়ার হয় মেরুদণ্ড। আজ হইতে প্রায় ৩৫ কোটি বৎসর পূর্বে অর্ডোভিসিয়ান উপযুগের শেষের দিকে প্রথম মেরুদণ্ডবিশিষ্ট যে সকল জীবের জন্ম হয়, তাহাদিগের এক দলকে বলা হয় মাছ।
মাছেরা সচরাচর কানকোর সাহায্যেই জল হইতে বাতাস সংগ্রহ করিয়া শ্বাসকার্য চালাইয়া থাকে। কিন্তু কালক্রমে কোনো কোনো মাছের আবার ফুসফুস গঠিত হইয়াছিল। এই ধরণের মাছ এখনও দেখিতে পাওয়া যায় আফ্রিকার সাগরে, যেমন– কোয়েলাকান্থ মাছ। ফুসফুসওয়ালা মাছেরা ডাঙ্গায় উঠিয়া পড়িলেও মারা যায় না, জল ও স্থল উভয় স্থানেই বাঁচিয়া। থাকিতে পারে।
যে সকল মাছ সমুদ্র উপকূলের কাছাকাছি বাস করিত, ঢেউয়ের আঘাতে বা জোয়ারের জলের সাথে তাহাদের কেহ কেহ ডাগায় উঠিয়া পড়িত। ইহাদের অনেকেই মরিয়া যাইত, কিন্তু সকলেই মরিত না। পরবর্তী ঢেউয়ের বা জোয়ারের জল আসা পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারিত। এইভাবে যে সকল মাছ জল ও ডাগায় বাঁচিয়া থাকার শক্তি অর্জন করিল, তাহারা হইল উভচর প্রাণী। ইহাদের বংশধর আজিকার কুমির, ব্যাঙ ইত্যাদি। উভচরদের সকলেরই ডাঙ্গার জীবন পছন্দ হয় নাই। কতক উভচর জন্তু আবার জলে বাস করিতে আরম্ভ করে। তাহাদের বর্তমান বংশধর তিমি, শুশুক ইত্যাদি।
উভচরদের কোনো কোনো শাখা স্থায়ীভাবে স্থলে বাস করিতে আরম্ভ করে। পরিবেশ পরিবর্তনের সাথে সাথে তাহাদের শরীরের নানা পরিবর্তন দেখা দেয়। তাহাদের লেজ আর চ্যাপ্টা থাকিল না, শল্ক হইল পশম এবং পাখনা হইল পা। এইভাবে ২৮ কোটি বৎসর পূর্বে। উভচর মৎস্যদের যে দলটি স্থায়ীভাবে ডাঙ্গাবাসী হইল, তাহাদের নাম হইল সরীসৃপ। জীব সৃষ্টির আদি হইতে আজ পর্যন্ত যত রকম জীব জন্মিয়াছে, তন্মধ্যে এই সরীসৃপরাই অতি বৃহৎ ও ভয়ানক। এই বিষয় পরে আলোচিত হইবে।
পুরাজীবীয় যুগের শেষ ভাগে ভূপৃষ্ঠে উদ্ভিদের সাতিশয় সমৃদ্ধি হইয়াছিল। সমুদ্রতীর ও জলাভূমিতে জন্মিয়াছিল নিবিড় অরণ্য। ভূপৃষ্ঠের আলোড়নে সেই নিবিড় অরণ্য মাটির নিচে চাপা পড়িয়া অত্যধিক চাপ ও তাপের প্রভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে কয়লায়। এই কারণে এই যুগটির নামকরণ হইয়াছে কার্বনিফেরাস। আজকাল আমরা যে পাথর কয়লা ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা এই যুগের অর্থাৎ ২৮ কোটি বৎসর আগের বৃক্ষদের দেহের ধ্বংসাবশেষ বা ফসিল।
খ. মধ্যজীবীয় যুগ (Mesozoic) এই যুগের গাছপালা, জীবজন্তু সবই ছিল অতিকায়। জীবজন্তুর মধ্যে সরীসৃপরাই ছিল সংখ্যায় বেশি এবং বিশালাকার। তাই এই যুগটিকে সরীসৃপদের যুগও বলা যায়। এই যুগটি ১৯ কোটি বৎসর আগে আরম্ভ হইয়া শেষ হইয়াছে ৭ কোটি বৎসর আগে।
এই যুগের নানাবিধ সরীসৃপের মধ্যে যে শ্রেণীর সরীসৃপেরা প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, তাহাদিগকে বলা হয় ডাইনোসর। এই ডাইনোসরের আবার কয়েকটি প্রকারভেদ আছে। যথা –ব্রন্টোসরাস, ট্রাইনোসরাস, অল্লোসরাস, গোগোসরাস, সেরাটোসরাস, স্টেগোসরাস ইত্যাদি।
একটি ব্রন্টোসরাসের দৈর্ঘ্য ছিল অন্তত ২৫ গজ এবং উহার ওজন ছিল ৫০ টন, অর্থাৎ ১,৩৫০ মণ। একটি ট্রাইরানোসরাসের ওজন ছিল প্রায় ১০ টন এবং লম্বায় ছিল ৫০ ফিটেরও বেশি।
আকৃতি ও প্রকৃতিতে পার্থক্য থাকিলেও ঐসকল সরীসৃপদের কতক বিষয়ে মিল ছিল। উহারা সকলেই পিছনের বিরাট পা ও লেজের উপর ভর দিয়া ছুটিত, সামনের ক্ষুদে ক্ষুদে থাবা দুইটি ব্যবহার করিত একমাত্র খাবার ও লড়াইয়ের জন্য এবং উহারা সকলেই ছিল মাংসাশী।
একদল সরীসৃপ আকাশে উড়িতে শুরু করিয়াছিল। ইহাদের বলা হয় টেরোডাকটিল। ইহাদের গায়ে পালক বা পশম ছিল না, ছিল শুধু চামড়ার ডানা ও ধারালো দাঁতওয়ালা মুখ (কতকটা বাদুড়ের ন্যায়)। মধ্যজীবীয় যুগের শেষের দিকে ক্রেটাশিয়াস উপযুগে, অর্থাৎ প্রায় ৮ কোটি বৎসর আগে টেরোডাকটিলেরা এইরূপ বিশালকায় হইয়াছিল যে, এক ডানার প্রান্ত হইতে আর এক ডানার প্রান্তের মাপ ছিল ২৫ ফিট। এই উড়ন্ত সরীসৃপরাই ছিল আধুনিক পাখির পূর্বপুরুষ। একই যুগেই দেখা যায় যে, ঐ উড়ন্ত সরীসৃপদের রূপান্তর হইতে আরম্ভ করিয়াছে এবং উহাতে পাখির লক্ষণ দেখা দিয়াছে। এইরূপ আর একটি উড়ন্ত জীব আর্কিওপটেরিক। এইটি পাখি ও সরীসৃপের মিশ্ররূপ — আধা পাখি, আধা সরীসৃপ।
আধুনিক সাপ, কুমির, গিরগিটি ইত্যাদির মতো সেই যুগের সরীসৃপরা ছিল ডিম্বপ্রসূ জীব। কিন্তু দেখা যায় যে, ট্রিয়াসিক উপযুগে অর্থাৎ আজ হইতে প্রায় ১৫ কোটি বৎসর আগে একদল ক্ষুদে ক্ষুদে জীব ডিম্ব প্রসব না করিয়া গর্ভধারণ ও বাচ্চা প্রসব করিত। এই সময় হইতেই স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাব হয়। বিশেষত সরীসৃপদের রক্ত ছিল ঠাণ্ডা, কিন্তু স্তন্যপায়ীদের রক্ত গরম।
মধ্যজীবীয় যুগের শেষের দিকে ক্রেটাশিয়াস উপযুগে ব্রন্টোসরাসাদি কোনো জাতের ডাইনোসরের চিহ্ন (ফসিল) পাওয়া যায় না। এইরূপ অতিকায়, মহাশক্তিশালী একটি জীবের সম্পূর্ণ জাতি ধ্বংস হওয়ার কারণ লইয়া জীববিজ্ঞানীদের অনেক আলোচনা চলিতেছে। কেহ বলেন, “বিপ্লব বা যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ডাইনোসরদের দৈহিক পরিবর্তন না হওয়ায় ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াইয়া চলিতে না পারায় ডাইনোসরেরা বংশরক্ষা করিতে পারে নাই।” কেহ বলেন, “মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে যেরূপ যৌবন ও বার্ধক্য আছে এবং বার্ধক্যে সন্তানোৎপাদিকা শক্তি থাকে না বা কমিয়া যায়, প্রত্যেক জীবের জাতিগত জীবনেও তদ্রুপ বার্ধক্য আছে এবং জাতিগত জীবনের বার্ধক্যেও ঐ জাতির সন্তানোৎপাদিকা শক্তি থাকে না বা কমিয়া যায়। মধ্যজীবীয় যুগের সরীসৃপ তথা ডাইনোসরদের জাতিগত জীবনের বার্ধক্য হেতুই উহারা সবংশে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।” ভূপৃষ্ঠে ডাইনোসরের একাধিপত্য ছিল প্রায় ১০ কোটি বৎসর।
অন্যান্য জীবদের বেলায় যাহাই ঘটিয়া থাকুক না কেন, স্তন্যপায়ীরা দুইটি বড় রকম সুবিধা পাইয়াছিল, যাহা অন্যান্য জীবদের ভিতর ছিল না। প্রথমত উষ্ণ রক্তের অধিকারী হওয়ায় স্তন্যপায়ী জীবেরা শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা বা যে কোনো রকম প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াইয়া নিতে পারিয়াছিল। দ্বিতীয়ত স্তন্যপায়ীদের সন্তানবাৎসল্য ছিল। অন্যান্য জীবদের মধ্যে এই দুইটির একটিও ছিল না। কাজেই অন্যান্য জীবগণকে পিছনে ফেলিয়া স্তন্যপায়ীরা উন্নতির পথে আগাইয়া চলিয়াছিল।
গ. নবজীবীয় যুগ (Caino zoic) আজ হইতে ৭ কোটি বৎসর পূর্বে এয়োসেন উপযুগের প্রথমেই দেখা যায় যে, স্তন্যপায়ী জীবগণ বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া অধিকাংশ ভূভাগ জুড়িয়া বসবাস করিতেছে। ঐ যুগের স্তন্যপায়ীগণ আকারে এখনকার স্তন্যপায়ী জীবের চেয়ে ছোট ছিল। বর্তমান যুগের হাতি, ঘোড়া, শূকর, গণ্ডার ইত্যাদি প্রাণীদের আদিপুরুষ ছিল একটি স্তন্যপায়ী জীব, উহার নাম ফেনাডোকাস। আকারে ইহা শিয়ালের চেয়ে বড় ছিল না।
হিংস্র ও মাংসাশী একদল স্তন্যপায়ী জীব ছিল, যাহার নাম ক্রিয়োডোন্ট। কালক্রমে এই ক্রিয়োডোন্টরা দুই দলে ভাগ হইয়া যায়। এক দলের চেহারা ছিল কুকুরের মতো, ইহাদের ক্রমবিবর্তনে কুকুর, নেকড়ে বাঘ, ভালুক ইত্যাদি এবং আর এক দলের চেহারা ছিল বিড়ালের মতো, ইহাদের ক্রমবিবর্তনে জন্মিয়াছে বিড়াল, বাঘ, সিংহ ইত্যাদি।
অন্যান্য স্তন্যপায়ীদের মধ্যে ছিল এক প্রকার ক্ষুদে ক্ষুদে জীব। ইহারা গাছে চড়িতে পারিত। ও ডালে ডালে লাফালাফি করিত।
নবজীবীয় যুগের প্রথম পর্বের সকল স্তন্যপায়ী জীব আজ বর্তমান নাই। কোনো কোনো দল লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, আবার কোনো কোনো নূতন দলের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। সাত কোটি বৎসর লাগিয়াছে উহাদের বর্তমান আকারে পৌঁছিতে।
যে সকল জীব মাটিতে, বিশেষত বনে-জঙ্গলে চলাফেরা করে, তাহাদের দৃষ্টিশক্তির চেয়ে ঘ্রাণশক্তি বেশি। কেন না, ঝোঁপ-জঙ্গলের বাধাজনিত কারণে দৃষ্টিশক্তি তত বেশি কাজে লাগে না। অদূরে ঝোঁপের আড়ালে কোনো শিকার থাকিলে ঘ্রাণের সাহায্যে তাহার অবস্থিতি জানিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে হয়। অথবা কোনো হিংস্র প্রাণী থাকিলেও তাহা ঘ্রাণের সাহায্যে জানিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতে হয়। অর্থাৎ আক্রমণ ও আত্মরক্ষা উভয়ের জন্যই ঘ্রাণশক্তি প্রখর হওয়া দরকার। কিন্তু বৃক্ষারোহী জীবদের ঘ্রাণশক্তি বিশেষ কোনো কাজেই আসে না। তাহাদের চাই প্রখর দৃষ্টিশক্তি। এক ডাল হইতে লাফাই আরেকটি ডাল ধরিতে হইলে চাই লক্ষ্যস্থলের দূরত্ব। ও অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করা, অন্যথায় জীবন বিপন্ন হইতে পারে। এইরূপ ক্রমিক চেষ্টার ফলে বৃক্ষারোহী জীবদের দৃষ্টিশক্তি উন্নততর হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু ও অক্ষিগোলকের অবস্থান পালটাইয়া যায়। অন্যান্য প্রাণীরা দুই চক্ষুতে একটি বস্তুর দুইটি ছবি দেখে। কিন্তু বৃক্ষরাহীদের চক্ষুর অবস্থান পরিবর্তিত হইয়া এরূপ হইল যে, উহারা দেখে একটি। ইহাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা কম।
চতুষ্পদ জন্তুর চারিটি পা-ই ব্যবহার করিতে হয় হাঁটার জন্য। কিন্তু বৃক্ষারোহীদের শাখা হইতে শাখান্তরে লাফালাফি করিতে সামনের পা দুইটি ব্যবহার করিতে হয় ধরার জন্য। এইরূপে উহাদের সামনের পা দুইটি হইল থাবা।
বৃক্ষারোহীদের আরো কয়েকটি বিষয়ে অভিজ্ঞতালাভ হইয়াছিল। ডালে ডালে লাফালাফি করিবার কালে প্রতি মুহূর্তে কর্তব্য নির্ধারণ অর্থাৎ লক্ষ্য স্থির করার জন্য দ্রুত মস্তিষ্ক চালনা। করিতে করিতে মস্তিষ্ক বড় হইতেছিল। অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সাথে সাথে পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়া হাঁটায় অভ্যস্ত হইয়াছিল এবং থাবা দুইটি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল আক্রমণ ও আত্মরক্ষার জন্য।
দুই পায়ে চলাফেরায় সুবিধা অনেক। ইহাতে সামনের পা দুইটি সব সময়ই থাকে মুক্ত। প্রথমত আঁচড়াইয়া-কামড়াইয়া শিকার ধরা বা আক্রমণকারী শত্রুর কবল হইতে রক্ষা পাওয়ার অপেক্ষা ডালপালার (লাঠির) ব্যবহার বহুগুণে উত্তম। দ্বিতীয়ত মুখের সাহায্যে খাদ্য আহরণের চেয়ে থাবার সাহায্যে খাদ্যদ্রব্য তুলিয়া মুখে দেওয়ায় শ্রান্তি কম এবং শান্তি বেশি। এইরূপ নানাবিধ সুবিধা পাইয়া একদল বৃক্ষারোহী জীব পুরামাত্রায় দ্বিপদ হইয়া উঠিল এবং উহাদের থাবা দুইটি পরিণত হইল হাতে।
থাবা ব্যবহার করে না, মুখের সাহায্যেই খাবার তুলিয়া লয় –এইরূপ চতুষ্পদ জন্তুদের প্রায় সকলেরই মুখমণ্ডল হয় লম্বাটে। যথা –গরু, ঘোড়া, শিয়াল, কুকুর ইত্যাদি। আর যাহারা থাবা ব্যবহার করে, এইরূপ জন্তুদের প্রায়ই মুখমণ্ডল হয় গোল। যথা –বাঘ, বিড়াল, সিংহ ইত্যাদি। দ্বিপদ জন্তুরা খাবার তুলিয়া মুখে দেওয়া ও মশা-মাছি তাড়াইবার কাজে হাত ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলে, তাহাদের মুখমণ্ডল হইতে থাকে গোল এবং মশা মাছি তাড়ানো ও ধূলাবালি ঝাড়া ইত্যাদি কোনো কাজে লেজের ব্যবহার না থাকায় লেজটি হইতে থাকে ছোট। কালক্রমে উহাদের মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্তে সামান্য একটু নমুনা ছাড়া লেজের আর কোনো চিহ্নই। থাকিল না। ইহাদের বলা হয় প্যারাপিথেকাস।
উক্তরূপে একটি অভিনব জন্তুর উদ্ভব হইলে, কালক্রমে উহারা আবার দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। উহাদের মধ্যে একটির লেজ নাই, মুখমণ্ডল ঈষৎ গোল, উহারা সোজা হইয়া হাঁটিতে পারে এবং যাবতীয় কাজে হাত ব্যবহার করে। এই জন্তুটি বানর নহে, শিম্পাঞ্জি, গরিলা বা ওরাংওটাং নহে এবং পুরাপুরি মানুষও নহে। ইংরাজিতে ইহাদিগকে বলা হয় অ্যানথ্রোপয়েড এপ বা মানুষসদৃশ বানর। ইহারাই মানুষের পূর্বপুরুষ। প্যারাপিথেকাসের অপর শাখার জন্ধুদের সাথে অ্যানথ্রোপয়েড এপ-এর চালচলন ও আকৃতিগত পার্থক্য সামান্য হইলেও তাহারা বনমানুষের পূর্বপুরুষ।[২৫]
ক্রমবিবর্তন কোনোটিই অল্প সময়ে হয় না। ক্ষুদ্র একবিন্দু প্রোটোপ্লাজম হইতে চোখের দেখায় চিনিতে পারার মতো জীবের সৃষ্টি হইতে, তুলতুলে শরীরে বর্মসাজ ও মেরুদণ্ড জন্মিতে সময় লাগিয়াছিল প্রায় একশত কোটি বৎসর এবং জলচর হইতে উভচর, স্থলচর, সরীসৃপ ও পশু (বানর) রূপ ধারণ করিয়া তাহার লেজ খসিতে সময় লাগিয়াছিল আরও প্রায় পঞ্চাশ কোটি বৎসর।
————
[২৪. পৃথিবীর ঠিকানা, অমল দাসগুপ্ত, পৃ. ১৯৪–১৯৮।
২৫. পৃথিবীর ঠিকানা, অমল দাসগুপ্ত, পৃ. ২১৮–২২৪।]
১০. আদিম মানবের সাক্ষ্য
আদিম মানবের সাক্ষ্য
প্রায় এক শতাব্দীকাল পর্যন্ত জীববিজ্ঞানীগণ চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন মানুষের পূর্বপুরুষের নিদর্শন পাওয়ার জন্য এবং এ ব্যাপারে তাহারা কতক সাফল্যও লাভ করিয়াছেন। বিভিন্ন অঞ্চলের মাটি খুঁড়িয়া বিভিন্ন সময়ে যে সকল বিক্ষিপ্ত হাড়গোড় এবং আস্ত কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহা সুসংবদ্ধভাবে সাজাইয়া মানুষের বিবর্তনের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বিজ্ঞানীরা পাইয়াছেন। উহাতে দেখা যায় যে, হাল আমল হইতে যতই অতীতের দিকে যাওয়া যায়, মানুষের চেহারা ততই বুনো হইয়া দাঁড়ায় এবং যতই বর্তমানের দিকে আসা যায়, ততই বুনো হয় আধুনিক। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখানো যাইতে পারে –অস্ট্রালোপিথেকাস মানুষ, জাভা ও পিকিং মানুষ, নেয়ানডার্থাল মানুষ, ক্রোমাঞ মানুষ ইত্যাদি।
অস্ট্রালোপিথেকাস মানুষ— আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিম ট্রান্সভাল অঞ্চলে ১৯২৪ সালে একটি মাটির ঢিবিকে ডিনামাইট দিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। উহার নিচে আরও কিছু মাটি খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছিল ছয় বৎসর বয়সের একটি ছেলের মাথার খুলি। উহার গড়ন ছিল বানর ও মানুষের মাঝামাঝি। খুলিটির বয়স ছিল এক লক্ষ বৎসরের কিছু বেশি। ইহাকে বলা হয় অস্ট্রালোপিথেকাস মানুষ।
১৯৩৬ সালে জোহানেসবার্গ-এর নিকটবর্তী স্থান হইতে মাটি খুঁড়িয়া আর একটি মাথার খুলি ও কিছু হাড়গোড় পাওয়া গিয়াছিল। এইগুলি ছিল একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের। এইটিও ছিল না। মানুষ, না বানর গোছের এবং অস্ট্রালোপিথেকাসের সমবয়সী ও সমগোত্রীয়।
১৯৩৮ সালে ঐ অঞ্চল হইতে আরও একটি মাথার খুলি ও কয়েকটি দাঁত এবং ১৯৪৭ সালে ঐ রকম আরও নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল। সবগুলিই ছিল মানুষ ও বানরের মাঝামাঝি চেহারার এবং প্রত্যেকের বয়সই ছিল লক্ষাধিক বৎসর।
জাভা ও পিকিং মানুষ –হল্যাণ্ডবাসী ইউজেন দুবোয়া নামক একজন ডাক্তার ১৮৯০-৯২ সালে জাভা দ্বীপের পূর্বার্ধে মাটি খুঁড়িয়া বিক্ষিপ্তভাবে পাইয়াছিলেন মানুষের একটি দাঁত সহ নিচের চোয়ালের একটি হাড়, উপরের চোয়ালের ডান দিকের একটি পেষণ দাঁত, মাথার খুলি ও উরুর একটি হাড়।
প্রোক্ত কঙ্কালগুলি পর্যবেক্ষণ করিয়া জীববিজ্ঞানীরা জানিয়াছেন যে, ব্রহ্মতালুটি বানরের মতো ও উরুর হাড় অবিকল মানুষের মতো। অর্থাৎ উহা আধা বানর ও আধা মানুষ। মাটির যে স্তরে ঐ কঙ্কালসমূহ পাওয়া গিয়াছে, তাহার পুরাতনত্বের হিসাবে ঐ কঙ্কালের বয়স এক লক্ষ হইতে তিন লক্ষ বৎসরের মধ্যে।
পিকিং শহরের নিকটবর্তী স্থান হইতে একজন জার্মান ডাক্তার ১৯০২ সালে আবিষ্কার করেন একটি দাঁত, ১৯১৬ সালে একজন জীববিজ্ঞানী ঐ অঞ্চলের মাটি খুঁড়িয়া প্রাপ্ত হন কতগুলি হাড়গোড়, ১৯২৭ সালে কানাডার একজন জীববিজ্ঞানী প্রাপ্ত হন একটি দাঁত এবং ঐ একই অঞ্চল হইতে একজন চীনা, একজন ফরাসী এবং একজন আমেরিকান জীববিজ্ঞানী খুঁজিয়া পান মাথার খুলি, চোয়ালের হাড় ও দাঁত ইত্যাদি। চেহারায় ঐ পিকিং মানুষগুলি জাভা মানুষের সমগোত্রীয় ও সমবয়সী। ইহারা না মানুষ, না বানর। অর্থাৎ মানুষ ও বানরের মাঝামাঝি চেহারা।
নেয়ানডার্থাল মানুষ –জার্মানীর ডুসেলডর্ফ ও এনবেরফেণ্ড-এর মাঝখানে নেয়ানডার্থাল নামক স্থানে ১৮৫৬ সালে মৃত্তিকা খনন করিয়া পাওয়া গিয়াছিল একটি মাথার খুলি। জীববিজ্ঞানীদের মতে খুলিটি মানুষের পূর্বপুরুষের। মাটির যে স্তরে ঐটি পাওয়া যায়, তাহার প্রাচীনত্বের হিসাবে ঐ খুলিটির বয়স ৭৫ হাজার বৎসর।
১৯০৮ সালের ৩ আগস্ট তারিখে ফ্রান্সের শাপেন ও-স্যা নামক গ্রামের কাছে একটি গুহা হইতে পাওয়া গিয়াছিল একটি আস্ত কঙ্কাল। এইটি পরীক্ষা করিয়া নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই কঙ্কালটি মানুষের। বিশেষত নেয়ানডার্থাল মানুষের সমবয়সী ও সমগোত্রীয়।
ঐ আস্ত ককালটি হইতে মানুষের একটি নিখুঁত ছবি পাওয়া গিয়াছে। মানুষটির মুণ্ড প্রকাণ্ড, ধড় ছোট, লম্বায় পাঁচ ফুট এক ইঞ্চি হইতে তিন ইঞ্চির মধ্যে। দুই পায়ে ভর দিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু শরীর ও মাথা সামনের দিকে নুইয়া পড়ে, হাঁটু বাকিয়া যায়। শরীরের তুলনায় মুখ বড়, মাথার খুলি চ্যাটালো। অর্থাৎ মানুষ নহে, পুরাপুরি বানরও নহে। তবে মানুষের আদলটিই বেশি।
ক্রো-মাঞঁ মানুষ –১৮৬৮ সালে ফ্রান্সের দোর্দোন অঞ্চলে পাঁচটি পূর্ণাবয়ব কঙ্কাল পাওয়া যায়। উহাকে বলা হয় ক্রোমাঞ (Cro-Magnon) মানুষ। লম্বায় ৫ ফিট ১১ ইঞ্চি হইতে ৬ ফিট ১ ইঞ্চির মধ্যে। ইহাদের লম্বাটে মাথা, থ্যাবড়া মুখ, পেশীবহুল প্রত্যঙ্গ, উঁচু চোয়াল। চেহারার দিক দিয়া পুরাপুরি আধুনিক মানুষ। কালগুলির বয়স মাত্র ৩০ হাজার বৎসর।[২৬]
জীববিজ্ঞানীগণ বলেন যে, পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাব হইয়াছে প্রায় দেড়শত কোটি বৎসর আগে। কিন্তু মানুষ বর্তমান মানুষের রূপ পাইয়াছে মাত্র ত্রিশ হাজার বৎসর আগে।
.
# মানুষ ও পশুতে সাদৃশ্য
ধর্মাচার্যগণ বলিয়া থাকেন যে, যাবতীয় জীবের মধ্যে মানুষ ঈশ্বরের শখের সৃষ্ট জীব এবং উহা পবিত্র মাটির তৈয়ারী। আকৃতি-প্রকৃতি ও জ্ঞানে-গুণে মানুষের সমতুল্য কোনো জীবই নাই। অর্থাৎ জীবজগতে মানুষ অতুলনীয় জীব। কিন্তু বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, জীবজগতে মানুষের তেমন কোনো বৈশিষ্ট নাই। আপাতদৃষ্টিতে যে সমস্ত বৈশিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইল ক্রমবিবর্তনের ফল। মৌলিক বৈশিষ্ট বিশেষ কিছুই নাই এবং যাবতীয় জীবদেহের মৌলিক উপাদান একই।
মানুষের রক্তের প্রধান উপাদান শ্বেত কণিকা, লোহিত কণিকা, জল ও লবণ জাতীয় পদার্থ এবং দেহ বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায় লৌহ, কার্বন, ফসফরাস ও গন্ধকাদি কতিপয় মৌলিক পদার্থ। দেখা যায় যে, অন্যান্য প্রাণীর দেহের উপাদানও উহাই।
জীবগণ আহার করে দেহের স্বাভাবিক ক্ষয় পুরণের জন্য। ইহাতে জানা যায় যে, শরীরের যে বস্তুটি ক্ষয় হইতেছে, তাহা পূরণ করিবার জন্যই আহাবের প্রয়োজন। জীবজগতে যখন খাদ্য-খাদক সম্পর্ক বর্তমান আছে, তখন উহাদের দেহগঠনের উপাদানও হইবে বহুল পরিমাণে এক। যেমন– বাঘ মানুষ ভক্ষণ করে, মানুষ মাছ আহার করে, আবার মাছেরা পোকা-মাকড় খাইয়া বঁচিয়া থাকে ইত্যাদি। ইহাতে বুঝা যায় যে, একের শরীরের ক্ষয়মান পদার্থ অপরের শরীরে বিদ্যমান আছে। মাতৃহীন শিশু যখন গোদুগ্ধ পানে জীবন ধাবণ করিতে পারে, তখন গাভী ও প্রসূতির দেহের উপাদান বহুলাংশে এক।
প্লেগ, জলাতঙ্ক প্রভৃতি রোগসমূহ ইতর প্রাণী হইতে মানবদেহে এবং মানবদেহ হইতে ইতর প্রাণীতে সংক্রমিত হইতে পারে। ইহাতে উহাদের টিস্যু (tissue) ও রক্তের সাদৃশ্য প্রমাণিত হয়।
চা, কফি ও মাদক জাতীয় দ্রব্যাদি গ্রহণে ও কতক বিষাক্ত দ্রব্য প্রয়োগে মানুষ ও পশুর একই লক্ষণ প্রকাশ পায়, ইহাতে উভয়ের পেশী (muscle) ও স্নায়ুর (nerve) সাদৃশ্য প্রমাণিত হয়।
গো-মহিষাদি পশুরা লোমশ প্রাণী, মানুষও তাহাই এবং পশুদের দেহে যেরূপ পরজীবী বাস করে, মানুষের শরীরেও তদ্রূপ উকুনাদি বাস করে। প্রজননকার্যে মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী জীবদের বিশেষ কোনো পার্থক্য নাই। পূর্বরাগ, যৌনমিলন, সূণোৎপাদন, সন্তান প্রসব ও প্রতিপালন সকলই প্রায় একরূপ।
স্তন্যপায়ী সকল জীবকেই রজঃশীলা হইতে দেখা যায়। তবে বিভিন্ন জীবের যৌবনে পৌঁছিবার বয়স, রজঃ-এর লক্ষণ ও স্থিতিকাল এবং গর্ভকাল এক নহে। তথাপি একজন মানবীর রজঃ বা ঋতুর অন্তর এক মাস (সাধারণত ২৮ দিন) এবং একটি বানরীরও এক মাস, আর একজন মানবীর গর্ভধারণকাল দশ মাস (সাধারণত নয় মাস) এবং একটি গাভীরও গর্ভধারণকাল ঐরূপ।
মানুষের ন্যায় পশু-পাখিরও সন্তানবাৎসল্য এবং সামাজিকতা আছে। মানুষ যেরূপ আহ, উহ, ইশ ইত্যাদি অনেক প্রকার শব্দ দ্বারা হর্ষ, বিষাদ, ভয়, ক্রোধ ইত্যাদি মানসিক ভাব ব্যক্ত করে, তদ্রূপ অনেক ইতর প্রাণীও কতক সাঙ্কেতিক শব্দ দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করিয়া থাকে। গৃহপালিত কুকুরের ঘেউ ঘেউ শব্দের পাঁচটি রকমভেদ আছে। ইহাতে শত্রুর আগমনের বার্তা, হর্ষের শব্দ, বেদনার শব্দ ইত্যাদি লক্ষিত হয়। গৃহপালিত মোরগ প্রায় বারোটি শব্দ ব্যবহার করে। গাভীর হাম্বা রবে তিন-চারি প্রকার মনোভাব প্রকাশিত হয়। ইতর প্রাণী কথা যে একেবারেই বলিতে পারে না, এমন নহে। ময়না, টিয়া, কাকাতুয়া ইত্যাদি পাখিরা মানুষের মতোই কথা বলিতে শেখে।
গরু, ঘোড়া, হাতি, বাঘ, শিয়াল, বিড়াল ইত্যাদি পশুরা পঞ্চ-ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট জীব, মানুষও তাহাই। ঐসকল পশুর এবং মানুষের রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি ইত্যাদিতে কোনো পার্থক্য তো নাই-ই, উহাদের অভ্যন্তরীণ দেহযন্ত্র যথা –হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, প্লীহা, যকৃত, মূত্রযন্ত্র, পাকস্থলী ইত্যাদির গঠন, ক্রিয়া, সংযোজন ও অবস্থিতি তুলনা করিলেও বিশেষ কোনো পার্থক্য লক্ষিত হয় না। বিশেষত শিম্পাঞ্জি, গরিলা ও বানরের সহিত মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতির সাদৃশ্য যথেষ্ট।
জীববিজ্ঞানীগণ স্তন্যপায়ী শ্রেণীর জীবসমূহকে কতগুলি দল বা বর্গ-এ বিভক্ত করিয়াছেন। উহার বিশেষ একটি বর্গের সমস্ত প্রাণীকে একত্রে বলা হয় প্রাইমেট (Primate)। যাহারা হাত দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া গাছে উঠিতে পারে, যাহাদের হাতে পাঁচটি করিয়া আঙ্গুল আছে, যাহাদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অন্যান্য আঙ্গুলগুলির উপর ন্যস্ত করা যাইতে পারে, যাহাদের আঙ্গুলে নখ থাকে, যাহাদের অক্ষিগোলক চতুর্দিকে অস্থি দ্বারা পরিবৃত, যাহাদের স্তনগ্ল্যাণ্ড বক্ষদেশে নিবদ্ধ এবং যাহাদের পাকস্থলী সাধারণভাবে গঠিত –তাহারাই প্রাইমেট বর্গের অন্তর্গত। দেখা যায় যে, মানুষের মধ্যে উহার প্রত্যেকটি চিহ্নই বিদ্যমান। সুতরাং মানুষ যে প্রাইমেট, সেই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।
তাহা হইলে মানুষের বৈশিষ্ট কোথায়?
.
# মানুষের বৈশিষ্ট
মানুষের সহিত অন্যান্য জীবদের তথা পশুদের শত শত রকম সামঞ্জস্য বিদ্যমান। কাজেই যাবতীয় জীব বিশেষত পশুরা মানুষের আত্মীয়, এ কথাটি অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তথাপি মানুষ মানুষই, পশু নহে। এখন দেখা যাক যে, অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে মানুষের তফাত কি।
জীবজগতে মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট তিনটি। যথা –হাত, মগজ ও ভাষা।
বিবর্তনের নিয়ম-কানুনে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কোনো কোনো বিষয়ে দ্বিমত থাকিলেও একটি বিষয়ে প্রায় সকল বিজ্ঞানীই একমত যে, মানুষের পূর্বপুরুষেরা এককালে পুরাপুরি বৃক্ষচারী জীব ছিল। কালক্রমে যখন তাহারা গাছের বাসা ছাড়িয়া মাটিতে নামিয়া আসিল, তখন অন্যান্য অনেক জানোয়ারের তুলনায় নানা দিক দিয়াই তাহারা ছিল অসহায়। জীবন সংগ্রামের জন্য ছিল তাহাদের প্রধানত দুইটি সম্বল। প্রথমত অন্যদের তুলনায় ভালো মস্তিষ্ক, দ্বিতীয়ত চলাফেরার কাজ হইতে মুক্তি পাওয়া’ দুইখানি হাত। ইহারই সাহায্যে মানুষ বাঁচিবার চেষ্টা করিয়াছে। ফলে উন্নত হইয়াছে মানুষের মস্তিষ্ক এবং হাত দুইই। মস্তিষ্কের উন্নতি হাতকে উন্নত করিয়াছে, আবার হাতের উন্নতি মস্তিষ্ককে উন্নত করিয়াছে। অধিকন্তু মস্তিষ্ক এবং হাত, এই দুইয়ের উপর নির্ভর করিয়া মানুষ কথা বলিতে শিখিয়াছে, ভাষা পাইয়াছে। এই ভাষা কাহারও একার সম্পত্তি নহে, পুরা সমাজের সম্পত্তি। তাই ভাষাভাষী হিসাবে মানুষ একান্তই সামাজিক জীব। উন্নত মস্তিষ্ক, কর্মক্ষম হাত এবং সুসমঞ্জস ভাষা সহায়ক হইল এক রকম জীবের — তাহারই নাম মানুষ। কিন্তু হাত, মগজ ও ভাষা জীবজগতের সর্বত্র দুর্লভ নহে। অনুন্নত জীবজগতের সর্বত্র দুর্লভ– মানুষের হাসি।
.
# বিবর্তনের কয়েকটি ধাপ
ক্রমবিবর্তনের বিষয়ে এযাবত যে সমস্ত আলোচনা করা হইল এবং তাহাতে যে সমস্ত জীবের নামোল্লেখ করা হইল, তাহা বিবর্তনের প্রধান প্রধান ধাপ মাত্র। এক জাতীয় জীবের আর এক জাতীয় জীবে রূপান্তরিত হইতে সময় লাগে লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি বৎসর এবং ইহারই মধ্যে ঐ জীবটি রূপান্তরিত হয় আরও শত শত জীবে। কিন্তু এই মধ্যবর্তী জীবগুলি প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াইতে পারার দরুন অথবা অন্য কোনো কারণে অধিকাংশই পৃথিবীর বুকে টিকিয়া থাকিতে পারে না, কৃচিৎ অনুন্নত অবস্থায় বাঁচিয়া থাকে। যেমন –আফ্রিকার কোয়েলাকান্থ ও ফুসফুসওয়ালা মাছ; ইহারা মৎস্য ও সরীসৃপের মাঝামাঝি জীব। যেমন– গরিলা; ইহারা পশু ও মানুষের মাঝামাঝি জীব। যেমন –আর্কিওপটেরিক; ইহারা পাখি ও সরীসৃপের মাঝামাঝি জীব ইত্যাদি। যাহা হউক, বিবর্তনের আলোচ্য প্রধান প্রধান ধাপগুলি সম্বন্ধে আর একবার সংক্ষেপে আলোচনা করিতেছি।
অ্যামিবা ইহারা এককোষী জীব। ইহার বিবর্তনে অর্থাৎ কোষ সমবায়ে গঠিত হইয়াছে বহুকোষী জীব।
বহুকোষী জীব ইহারা দুই দলে বিভক্ত হইয়া এক দল হইতে অচল উদ্ভিদ এবং অপর দল হইতে জন্মিয়াছে সচল জীব।
সচল জীব ইহাদের এক শ্রেণীর জীবের নাম ট্রাইলোবাইট।
ট্রাইলোবাইট ইহারা পোকা জাতীয় জলজীব। কালক্রমে ইহাদের এক শ্রেণীর দেহে মেরুদণ্ড জন্মে, তাহাদের বলা হয় মাছ।
মাছ ইহাদের বংশ হইতে জন্মে জলচর, উভচর, বিহঙ্গম ও স্থলচর সরীসৃপ।
সরীসৃপ ইহাদের এক শাখা হইতে জন্মে উষ্ণ রক্ত বিশিষ্ট স্তন্যপায়ী জীব।
স্তন্যপায়ী জীব ইহাদের এক শাখা হয় বৃক্ষচারী জীব, তাহাদের বলা হয় প্রাইমেট।
প্রাইমেট ইহাদের মধ্যে জন্মে দ্বিপদ জীব, যাহাদের বলা হয় প্যারাপিথেকাস।
প্যারাপিথেকাস ইহাদের মধ্য হইতে একদল জন্মে পুরাপুরি সমতলভূমিবাসী দ্বিপদ জীব। ইহাদের বলা হয় এ্যানথ্রোপয়েড এপ বা বনমানুষ।
বনমানুষ ইহাদের ক্রমোন্নতির ফলে জন্মিয়াছে অসভ্য ও আধুনিক সভ্য মানুষ।
————
[২৬. পৃথিবীর ঠিকানা, অমল দাসগুপ্ত, পৃ. ২৬১।]
১১. বংশগতি
বংশগতি
জীবের বংশপ্রবাহ
জীববিজ্ঞানীগণ বলেন যে, পৃথিবীর যাবতীয় জীবদেহই কোষ বা সেল সমবায়ে গঠিত। অ্যামিবার মতো এককোষবিশিষ্ট জীবেরা বংশবৃদ্ধি করে নিজেকে দুই ভাগ করিয়া। এই ভাগ হওয়াটিকে বলা হয় বিভাজন। বিভাজনের প্রণালী বা কোষাভ্যন্তরের কাণ্ডকারখানা কিছু জটিল। তাই উহার জটিলতাকে বাদ দিয়া আমাদের শুধু এইটুকু জানিয়া রাখা ভালো যে, কোষগুলি পুষ্টিকর আহার পাইলে যথাসময়ে ফাটিয়া যায় ও একটি কোষ দুইটি পূর্ণাঙ্গ কোষে পরিণত হয়। এইরূপে চলিতে থাকে জীবাণুদের বংশবৃদ্ধি।
জীবাণুদের বংশবৃদ্ধির কাজে সময় বেশি লাগে না। কোনো কোনো জীবাণু আশ্চর্য রকম বংশবৃদ্ধি করিতে পারে। প্যারামেসিয়ান নামক প্রোটোজোয়া জাতীয় জীবাণুর সেল এক ইঞ্চির একশত ভাগের এক ভাগের চেয়ে বেশি বড় নহে। তাহার একটি মাত্র জীবাণু লইয়া এক বাটি জলের মধ্যে যদি ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তবে সাত দিন পরে গণনা করিলে দেখা যাইবে যে, সেই একটি হইতে জীবাণু জন্মিয়াছে প্রায় দশ লক্ষ। অধিকাংশ রোগের জীবাণুরা এই রকম বা ইহার অপেক্ষাও বেশি বংশবৃদ্ধি করিয়া থাকে।
এককোষী জীবেরা যেমন নিজেকে দুই ভাগ করিয়া বংশবৃদ্ধি করিতে পারে, বহুকোষী জীবেরা তাহা পারে না। বহুকোষী জীব যথা –কীট, পতঙ্গ ইত্যাদির দেহের কোষগুলি দুই জাতীয়। যথা– দেহকোষ এবং জননকোষ। জননকোষগুলি আবার দুই জাতীয়। যথা –পুং জননকোষ এবং স্ত্রী জননকোষ বা ডিম্বকোষ।
দেহকোষ ও জননকোষের বিভাজন প্রণালী একই, অর্থাৎ একটি কোষ বিভক্ত হইয়া দুইটি, দুইটি হইতে চারিটি এবং তাহা হইতে আটটি –এইরূপ সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়া থাকে। ব্যতিক্রম হইল এই যে, দেহকোষ বিভক্ত হওয়ার ফলে ঐ জীবটির দেহের বৃদ্ধি বা পুষ্টি হয় এবং জননকোষ বিভক্ত হইয়া জন্ম হয় ঐ জীবটির সদৃশ আর একটি স্বতন্ত্র জীবের। কিন্তু জননকোষদ্বয় একা একা বিভক্ত হইতে পারে না। ইহাতে আবশ্যক হয় পুং জননকোষ ও ডিম্বকোষের লন। এই মিলনকে বলা হয় যৌনক্রিয়া।
মানুষ, পশু, পাখি ইত্যাদি উন্নত পর্যায়ের জীবসমূহের স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে এবং উহারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া যৌনক্রিয়া সম্পাদন করে। কিন্তু জোক, কেঁচো ও শামুকাদি নিম্নস্তরের জীবের ও অধিকাংশ উদ্ভিদের দেহে দুই জাতীয় কোষ মজুত থাকে এবং জল, বায়ু, মাছি ইত্যাদির দ্বারা ঐ দুই জাতীয় কোষের মিলন সাধিত হয়। মিলনমুহূর্তের পর হইতেই আরম্ভ হয় মিলিত কোষটির বিভাজন এবং বিভক্ত হইতে হইতে জন্ম হয় একটি পূর্ণাঙ্গ (সদৃশ) জীব বা উদ্ভিদ-এর।
যতদিন পর্যন্ত এককোষী জীবেরা নিজেদের কেবল দুই ভাগ করিয়া বংশবৃদ্ধি করিত, ততদিন পর্যন্ত জীবজগতে বিশেষ কোনো বৈচিত্র দেখা দেয় নাই। যখন হইতে স্ত্রী-পুরুষ দুইজনের মিলনে বংশবৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল, তখন হইতে প্রাণীজগতে শুরু হইল নানা পরিবর্তন ও দ্রুত উন্নতি। একটি কোষকে সমান দুই ভাগ করিলে, খণ্ড দুইটি জনয়িতার হুবহু নকল হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু যে স্থলে জনক ও জননী- দুইটি স্বতন্ত্র ব্যক্তি হইতে সন্তানের জন্ম, সেই স্থলে জন্মদাতাদের সঙ্গে সন্তানের ঐকান্তিক মিল তো থাকিতেই পারে না, বরং সন্তানদের পরস্পরের মধ্যেও পার্থক্য থাকে যথেষ্ট। জীবজগতের এতোধিক বৈচিত্রের মূল কারণও হইল যৌন প্রণালীতে বংশবৃদ্ধি।
অতি সাধারণভাবে জীবজগতের বৈচিত্র প্রকাশের কারণ বলা হইল। এখন প্রশ্ন থাকিল এই যে, জীবজন্তুর শরীরে এত রকমের ইন্দ্রিয়, অবয়ব ও যন্ত্রাদির সৃষ্টি হইল কি রকম? এই বিষয়ে বিজ্ঞানীগণ যাহা বলেন, তাহার সারমর্ম এই যে, পৃথিবীর আদিম অবস্থায় কেবল জলজন্তুই ছিল। অ্যামিবা পর্যায় অতিক্রম করিয়া যখন বহুকোষী জলজীব দেখা দিল, তখন তাহারা স্থিরভাবে জলে ভাসিয়া না থাকিয়া কোনো একদিকে জল ঠেলিয়া যাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। সেই অবস্থায় তাহাদের সামনের দিকের সেলগুলি প্রথম খাবারের সন্ধান পাইতে লাগিল, এবং বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে সর্বপ্রথম তাহাদের সংঘর্ষ হইতে লাগিল। তাই সামনের দিকের সেলগুলি খাবার সংগ্রহ, শত্রুকে এড়ানো বা দমন করা, দিক নির্ণয় করা প্রভৃতি কাজের ভার লইয়া নিজেদেরকে বিশেষভাবে ঐ কাজের উপযোগী করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই চেষ্টার ফলে জীবদেহে আস্তে আস্তে গড়িয়া উঠিল মস্তিষ্ক। প্রথমে আহার্য দ্রব্য ভিতরে নিবার জন্য মুখগহ্বর ও গলনালী, পরে চোখ, কান প্রভৃতি বাহেন্দ্রিয়গুলি এবং সঙ্গে সঙ্গে মগজ দেখা দিল। পারিপার্শ্বিক অবস্থার ভিন্নতা বা পরিবর্তন অনুসারে জীবদেহের এই সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৈশিষ্টও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আর প্রয়োজনবোধে প্রকাশ পাইল লেজ, ডানা, হাত, পা প্রভৃতি বহিরঙ্গগুলি।
বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, প্রাণীজগতের বিবর্তনের শুরুতে যে রকম করিয়াই ভিন্ন ভিন্ন জাতির উৎপত্তি হইয়া থাকুক না কেন, বর্তমানে উহার জাতীয়তা রক্ষার কারক সেলের অভ্যন্তরস্থ ক্রোমোসোম। কোনো কোনো জাতের সেল সহজ দৃষ্টিতেই দেখা যায়, আবার কোনো কোনো সেল এত ছোট যে, উহার ২৫০০টি সেল এক সারিতে সাজাইলে এক ইঞ্চির বেশি লম্বা হয় না। এত ছোট সেলের ভিতরটি কিন্তু ফুটবলের মতো শূন্যগর্ভ নহে, সেখানে আছে বহু পদার্থ, যাহা ভাবী জীবের জাতি ও প্রত্যঙ্গাদি সৃষ্টির কারক। সেলের মধ্যে ঐ ধরণের একটি পদার্থ ক্রোমোসোম। এই ক্রোমোসোমই জীবের জাতিভেদের জন্য দায়ী।
বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, প্রত্যেক ধাতব পদার্থের পরমাণুতে নির্দিষ্ট সংখ্যক ইলেকট্রন ও প্রোটন থাকে। যেমন –সোনায় ৭৯, রূপায় ৪৭, লোহায় ২৬ ইত্যাদি। একটি পরমাণুতে ৮০টি ইলেকট্রন বা প্রোটন আছে, এইরূপ সোনা জগতে মিলিবে না। কেননা, ঐরূপ সংখ্যা থাকিলে তাহা হইবে পারদ। জীবজগতেও ঐ রকম প্রত্যেক জাতীয় জীবের দেহকোষ বা জননকোষের মধ্যে এক। নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে, কোথায়ও উহার ব্যতিক্রম হয় না। ধাতব পদার্থের মৌলিকত্ব নির্ভর করে যেমন তাহার পরমাণুর ইলেকট্রন-প্রোটনের সংখ্যার উপর, জীবের জাতীয়তা নির্ভর করে তেমন তাহার দেহের সেলের ক্রোমোসোমের সংখ্যার উপর। কয়েক জাতীয় সেলের ক্রোমোসোমের সংখ্যা দেওয়া গেল।
উদ্ভিদ জীব
বাঁধাকপি – ১৮ গরু – ১৬
ভুট্টা – ২০ কুকুর – ২২
ধান – ২৪ ব্যাঙ – ২৬ মানুষ – ৪৬
গম – ৪২ ঘোড়া – ৩৮ বাঁদর – ৫৪
মানুষের শরীরের যে কোনো অংশের সেল অণুবীক্ষণের সাহায্যে দেখিলে দেখা যাইবে যে, উহার প্রত্যেকটি সেলে ৪৬টি করিয়া (আগে বলা হইত ৪৮টি) ক্রোমোসোম আছে। এক জাতীয় জীবের মধ্যে ক্রোমোসোমের সংখ্যার কখনও ব্যতিক্রম হয় না। জাতি ভেদে সংখ্যার তারতম্য হয় বটে।[২৭]
.
# মানুষের জন্ম প্রকরণ
ভ্রূণ সৃষ্টি
পুরুষের প্রধান জননেন্দ্রিয়ের নাম শুক্রাশয় (Testes)। ইহার ভিতর পাশাপাশি বীচির মতো দুইটি গ্ল্যাণ্ড আছে। গ্ল্যাণ্ডের ভিতরের স্তরের সেলগুলির কাজ –ক্রমাগত ভাগ হইয়া নূতন সেল তৈয়ার করা। সেগুলি দেখিতে ব্যাঙাচির মতো, কিন্তু এত ছোট যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না। এই সেলগুলির নাম জননকোষ বা পুং জার্মসেল। ইহারা শুক্রাশয়ের ভিতরে যথেচ্ছ সঁতরাইয়া বেড়ায়। শুক্রাশয়ের সাথে দুইটি সরু নল দিয়া মূত্রনালীর যোগ আছে। দরকারের সময়। জার্মসেলগুলি ঐ নল বাহিয়া মূত্রনালীর ভিতর দিয়া বাহিরে আসিতে পারে।
নারীর শরীরের ব্যবস্থা অন্য রকম। তাহার প্রধান জননেন্দ্রিয় ওভারিদ্বয় (Ovaries) তলপেটের ভিতরে ছোট দুইটি গ্ল্যাণ্ড। উহাদের ভিতরে নির্দিষ্ট সময়ে (পুরুষের মতো সব সময় নহে) একটি করিয়া (পুরুষের মতো অসংখ্য নহে) ডিম্বকোষ বা স্ত্রী জার্মসেল প্রস্তুত হয়। ডিম্বকোষ পুরুষদের জননকোষের তুলনায় অনেক বড়। ওভারির ভিতরে ডিম্বকোষ প্রস্তুত হইয়া পূর্ণতা লাভ করিলেই উহা নলের ভিতর দিয়া জরায়ুতে নামিয়া আসে। জরায়ু শক্ত রবারের মতো একটি থলি। সাধারণ অবস্থায় উহা মাত্র ৩ ইঞ্চি লম্বা। কিন্তু প্রয়োজনমতো যথেচ্ছ বড় হইতে পারে।
স্ত্রী-পুরুষের মিলনের সময়ে পুরুষের অসংখ্য জামসেল স্ত্রীঅগ দিয়া প্রবেশ করিয়া জরায়ুর ভিতরে ঢুকে। সেখানে স্ত্রীর ডিম্বকোষ তৈয়ারী থাকে উহাদের অভ্যর্থনার জন্য। জার্মসেল বা শুক্রকীটগুলি জরায়ুতে প্রবেশ করিয়াই লেজ নাড়িয়া (ব্যাঙাচির মতো ইহাদের লেজ থাকে) সাঁতার কাটিয়া ডিম্বকোষের দিকে ছুটিয়া আসে। উহাদের মধ্যে মাত্র একটিই ডিম্বকোষের ভিতরে ঢুকিতে পারে, কেননা একটি ঢুকা মাত্রই ডিম্বকোষের বাহিরের পর্দায় এমন পরিবর্তন ঘটে যে, অন্য কোনো শুক্রকীট আর ঢুকিতে পারে না। ডিম্বকোষের মধ্যে ঢুকিবার সময়ে শুক্রকীটের লেজটি খসিয়া বাহিরে থাকিয়া যায়।
মানুষের বেলায় সচরাচর প্রতি মাসে নির্দিষ্ট দিনে একটি করিয়া ডিম্বকোষ স্ত্রীলোকের ওভারিতে প্রস্তুত হইয়া জরায়ুমধ্যে শুক্রকীটের আগমনের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। কোনো জন্তুর তিন মাস, কোনো জন্তুর ছয় মাস, কাহারও বা বৎসরান্তে একবার ডিম্বকোষ জন্মে। যদি সেই সময় পুরুষ জামসেলের সঙ্গে উহার মিলন না হয়, তবে দুই-চারি দিনের মধ্যেই। ডিম্বকোষটি শুকাইয়া মরিয়া যায়। আবার যথাসময়ে (ঋতুতে) আর একটি প্রস্তুত হয়।
পুরুষ ও স্ত্রী সেলের মিলন হইলে মিলনের পরমুহূর্ত হইতে ডিম্বকোষের মধ্যে আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটিতে থাকে। স্ত্রী জার্মসেলের মধ্যে ঢুকিবার পর পুরুষ জার্মসেল অর্থাৎ শুক্রকীটের কোষকেন্দ্র আরও বড় হইতে থাকে এবং খানিক বড় হইয়া স্ত্রী জার্মসেলের কোষকেন্দ্রের সঙ্গে একেবারে মিশিয়া যায়। নানা বৈচিত্রময় পরিবর্তনের পর আরম্ভ হয় বিভাজন। একটি হইতে দুইটি, দুইটি হইতে চারিটি এবং তাহা হইতে আটটি –এইভাবে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া তিন সপ্তাহের মধ্যে ডিম্বকোষ সংখ্যায় বাড়িয়া গিয়া আয়তনে এত বড় হয় যে, তখন ভুণ বলিয়া তাহাকে চেনা যায়। মানুষের বেলায় শরীরের সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গই পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে স্পষ্ট ফুটিয়া উঠে। কিন্তু তখনও উহা ১ ইঞ্চির বেশি বড় হয় না। দুই মাস পরে পুরা এক ইঞ্চি হয় এবং তখন হইতে উহাকে মানুষের ভূণ বলিয়া চেনা যায়। পুরাপুরি শিশুর মতো হইতে সময় লাগে আরও সাত মাস। ন্যূনাধিক নয় মাস (চলিত কথায় দশ মাস) পর জরায়ু বা মাতৃজঠর ত্যাগ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয় মানবশিশু।
নারী ও পুরুষের মিলনের অর্থই হইল শুক্রকীট ও ডিম্বকোষের মিলন সাধন। নারী ও পুরুষের রতিক্রিয়া ব্যতীতও যৌনমিলন সম্ভব হইতে পারে। ইহাতে কোনো পুরুষের বীর্য ধারণপূর্বক তাহা যথাসময়ে কোনো কৌশলে নারীর জরায়ুমধ্যে প্রবেশ করাইয়া যৌনমিলন অর্থাৎ শুক্রকীট ও ডিম্বকোষের মিলন ঘটাইতে পারা যায় এবং তাহাতে সন্তানোৎপত্তি হইতে পারে। কিন্তু কোনো প্রকারের যৌনমিলন ব্যতীত সন্তানোৎপত্তি হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব।
ধর্মজগতে এমন কতগুলি আখ্যায়িকা প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহা প্রোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম। শুনা যায় যে, কামোত্তেজনাবশত কোনো মহাপুরুষের বীর্যস্থলন হইলে, উহা কোনো পাত্রে রাখা হইল এবং ঐ পাত্ৰমধ্যে সন্তান জন্সিল, অথবা কোনো ইতর জীবে উহা ভক্ষণ করিল, আর ঐ ইতর জীবের উদরে (জরায়ুতে নহে) সন্তান জন্মিল ইত্যাদি। আবার কোনো রমণী কোনো পুরুষকে স্বপ্নে দেখিয়া বা কাহাকেও চুমা খাইয়া কিংবা কোনো স্বর্গীয় দূতের বাণী শ্রবণ করিয়াই গর্ভবতী হইল ও সন্তান প্রসব করিল ইত্যাদি। ইহাতে কোনো নারী ও পুরুষ অর্থাৎ শুক্রকীট ও ডিম্বকোষের মিলনের আবশ্যক হইল না। কিন্তু এই জাতীয় অলৌকিক কাহিনীগুলি বিশ্লেষণ করিলে কোনো কোনোটিকে মনে হয় যে, উহা অলীক কল্পনা এবং কোনো কোনোটিতে পাওয়া যায় লৌকিকতার আভাস।
রামায়ণোক্ত সীতাকে বলা হয় অযযানিসম্ভবা। কেননা, তাহার নাকি মাতা ও পিতা কিছুই নাই এবং বাইবেলোক্ত যীশু খ্রীস্টকে বলা হয় অশিশ্নসম্ভব। কেননা, তাহার মাতা আছেন, পিতা নাই। কিন্তু উভয়ত আবার কিংবদন্তীও আছে। কোনো কোনো মতে –সীতা নাকি লঙ্কেশ্বর রাবণের কন্যা। ঐ কন্যাটি জমিলে কোনো গণক রাবণকে নাকি বলিয়াছিলেন যে, ঐ কন্যাটির উপলক্ষে তাহার মৃত্যু হইবে। তজ্জন্য রাবণরাজ কন্যাটিকে কোনো পাত্রে রাখিয়া সমুদ্রজলে ভাসাইয়া দেন এবং কোনো রকমে কন্যাসহ ঐ পাত্রটি মিথিলার রাজা জনকের হস্তগত হইলে তিনি ঐ কন্যাটিকে প্রতিপালন করেন ও রামের নিকট বিবাহ দেন ইত্যাদি।
যীশু খ্রীস্টের আবির্ভাবের সময়ে সখরিয়া (হজরত জাকারিয়া) নামক জনৈক ব্যক্তি ছিলেন ইহুদিদের ধর্মযাজক ও জেরুজালেম মন্দিরের সেবাইত বা পুরোহিত। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান, কারণ তাঁহার স্ত্রী ইলীশাবেত ছিলেন বন্ধ্যা। তাই শতাধিক বৎসর বয়সেও সখরিয়ার কোনো সন্তান ছিল না।
শুনা যায় যে, যীশুর মাতা মরিয়মকে তাঁহার পিতা এমরান মরিয়মের তিন বৎসর বয়সের সময়ে জেরুজালেম মন্দিরের সেবাকার্যের জন্য প্রেরণ করেন এবং সেখানে তিনি সখরিয়া কর্তৃক প্রতিপালিত হন।
সখরিয়া তাহার ১২০ বৎসর বয়সের সময়ে স্বর্গীয় দূতের মারফতে পুত্রবর প্রাপ্ত হন ও তাহাতে ইলীশাবেত গর্ভবতী হন এবং ইহার ছয় মাস পরে অবিবাহিতা মরিয়মও ১৬ বৎসর বয়সে স্বর্গীয় দূতের মারফত পুত্রবরপ্রাপ্ত হইয়া গর্ভবতী হন। যথাসময়ে ইলীশাবেত এক পুত্র প্রসব করেন এবং তাহার নাম রাখা হয় যোহন (হজরত ইয়াহইয়া)।
অবিবাহিতা মরিয়ম সখরিয়ার আশ্রমে থাকিয়া গর্ভবতী হইলে লোকলজ্জার ভয়ে ধর্মমন্দির ত্যাগ করিয়া নিজ জ্ঞাতিভ্রাতা যোসেফ (ইউসুফ)-এর সঙ্গে জেরুজালেমের নিকটবর্তী বয়তুল হাম নামক স্থানে অবস্থান করেন। এই স্থানে যথাসময়ে এক শুষ্ক খজুরবৃক্ষের ছায়ায় যীশু খ্রীস্ট (হজরত ঈসা আ.) ভূমিষ্ঠ হন।
কুমারী মরিয়ম এক পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন, ইহা জানিতে পারিয়া তাহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিতে থাকে এবং তাহারা মরিয়মের পালক পিতা সুবৃদ্ধ সখরিয়ার উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করিয়া তাহাকে হত্যা করিতে ধাবিত হয় এবং সখরিয়া এক বৃক্ষকোটরে লুকাইয়া থাকেন। কিন্তু ইহুদিগণ খোঁজ পাইয়া করাত দ্বারা ঐ বৃক্ষটি ছেদন করার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ সখরিয়া দ্বিখণ্ডিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন।[২৮]
ইহুদি ধর্মের বিধানমতে, ব্যভিচার ও নরহত্যা– এই উভয়বিধ অপরাধের শাস্তিই হইল প্রাণদণ্ড। এইখানে ব্যভিচারের অপরাধে বা অপবাদে সখরিয়ার প্রাণদণ্ডের বিষয় জানা যায় বটে, কিন্তু সখরিয়াকে বধ করার অপরাধে কোনো ইহুদির প্রাণদণ্ডের বিষয় জানা যায় না।
নারী ও পুরুষ
সৃষ্টি বলা হইয়াছে যে, মানুষের জীবকোষে ক্রোমোসোম থাকে ৪৬টি। কিন্তু ইহারা সবই এক ধরণের নহে। ইহাদের মধ্যে এক বিশেষ ধরণের ক্রোমোসোম আছে, যাহাদের বলা হয় সেক্স ক্রোমোসোম। ইহাদের মধ্যে আবার দুইটি ভাগ আছে। যথা –এক্স (X) ক্রোমোসোম এবং ওয়াই (Y) ক্রোমোসোম। পুরুষের জার্মসেলে এক্স ক্রোমোসোম সব সময় একটিই থাকে, কিন্তু স্ত্রীলোকের ডিম্বকোষ বা এগসেলে থাকে কখনও একটি এবং কখনও দুইটি করিয়া। ওয়াই ক্রোমোসোম শুধু পুরুষেরই থাকে, স্ত্রীলোকের সেলে কখনও থাকে না।
যখন কোনো ডিম্বকোষে দুইটি এক্স ক্রোমোসোম থাকে, এবং তাহা হইতে সূণের উৎপত্তি হয়, তখন তাহা হইতে জন্মে নারী এবং ডিম্বকোষে একটি এক্স ক্রোমোসোম থাকিয়া ভূণের উৎপত্তি হইলে, তাহাতে জন্মে পুরুষ।
যমজ সন্তান সৃষ্টি
ছাগ, মেষ, কুকুর, বিড়াল ও শৃগালাদি পশুরা এক সময়ে দুই, তিন বা চারি-পাঁচটি করিয়া সন্তান প্রসব করে, ইহাতে কোনোরূপ কথোপকথন বা হৈ চৈ হয় না। কেননা, উহা চলতি ঘটনা। কিন্তু মানুষের একবারের গর্ভে ঐরূপ সন্তান জন্মিলে পাড়া, দেশ, এমনকি সময় সময় জগতময় সাড়া পড়িয়া যায়। ক্যানাডার ডিওন পরিবারে এক রমণীর এক গর্ভে পাঁচটি কন্যা জন্মিয়াছিল এবং উহা দেশে-বিদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। কেননা ঐ পাঁচটি কন্যাই নাকি বাঁচিয়া ছিল ও পূর্ণবয়স্কা হইয়াছিল। তবে সচরাচর দেখা যায় যে, দুইয়ের অধিক যমজ সন্তানরা হয়তো মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়, নচেৎ ভূমিষ্ঠ হইয়া মারা যায়।
একেবারে গোড়ার অ্যামিবার মতো জীবের দিকটা বাদ দিয়া অপেক্ষাকৃত উন্নত শ্রেণীর জীবের দিকে চাহিলে আমরা দেখিতে পাই যে উহারা হয়তো ডিম্বপ্রসূ, নয়তো বাচ্চাপ্রসূ। ডিম্বপ্রসূদের মধ্যে আবার নানা রকম ডিমের সংখ্যা। যেমন– মাছেরা এক বারে হাজার হাজার, হাঁস-মুরগি পাঁচ-দশ গণ্ডা; কিন্তু কবুতরেরা মাত্র দুইটি ডিম্ব প্রসব করে। মানুষ কিংবা পশুরা ঐরূপ ডিম্ব প্রসব করে না বটে, কিন্তু আসলে উহারাও ডিম্বপ্রসূ জীব। পার্থক্য এই যে, আমরা যাহাদের ডিম্বপ্রসূ বলি, তাহারা সদ্য ডিম্ব প্রসব করে এবং ডিম্ব হইতে বাচ্চা জন্মে বাহিরে থাকিয়া, আর বাচ্চাপ্রসূদের ডিম্ব হইতে বাচ্চা জন্মে গর্ভে অর্থাৎ জরায়ুর ভিতরে থাকিয়া। ডিম্ব অথবা বাচ্চা –মায়েরা যাহাই প্রসব করুক, আসলে ডিমের সংখ্যার উপর নির্ভর করে বাচ্চাদের সংখ্যা।
সাধারণত মানুষের ডিম্বাধারে যথাসময়ে একটি ডিম্বই জন্মে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক ডিম্বও জন্মিয়া থাকে। মানুষের যখন যমজ সন্তান জন্মে, যে কারণেই হউক, তখন গর্ভিনীর গর্ভাধারে ডিম্ব জন্মে দুইটি এবং তখন পুরুষের মিলনে যদি ঐ দুইটি ডিম্বই নিষিক্ত হয়, তবে উহাতে সন্তান জন্মে দুইটি। অনুরূপভাবে তিন, চারি বা পাঁচটি ডিম্ব জন্মিলে সন্তানও জন্মে ঐ কয়টি। বৃটেনে নাকি হাজার করা এক গর্ভে তিনটি সন্তান জন্মিয়া থাকে। ততোধিক সন্তান হওয়া খুবই বিরল, তবে অসম্ভব নহে।
যমজ দুই প্রকার। যথা –অসম যমজ ও সম যমজ।
অসম যমজ –যদি কখনও কোনো নারীর ডিম্বাধারে একই সময়ে দুই বা ততোধিক ডিম্ব জন্মে এবং উহা পুরুষের মিলনে প্রাণবন্ত হয়, তবে যে যমজ সন্তান জন্মে, তাহাকে বলা হয় অসম যমজ।
অসম যমজ সন্তানেরা জরায়ুমধ্যে আলাদা আলাদা ডিম্ব হইতে আলাদা আলাদা ভুণে পরিণত হয় এবং উহাদের ফুল (Placenta) থাকে পৃথক পৃথক, অর্থাৎ যতটি সন্তান জন্মে ততটি। উহারা ভিন্ন ভিন্ন ভূণঝিল্লির ভিতরে বর্ধিত হয়। সন্তানেরা সকলে পুত্র বা সকলে কন্যা অথবা কতক পুত্র, কতক কন্যা হইতে পারে। সন্তানদের দৈহিক চেহারায় ও মানসিক বৃত্তিসমূহে অন্যান্য ভাই-ভগিনীর চেয়ে বেশি মিল থাকে না।
সম যমজ– যদি কখনও কোনো স্ত্রীলোকের একটি ডিম্ব জন্মিয়া শুক্রকীট যুক্ত হইবার পর কোনো কারণে দুই বা ততোধিক খণ্ডে খণ্ডিত হইয়া পড়ে, তবে উহার প্রত্যেক খণ্ড হইতে এক একটি সন্তান জন্মিতে পারে। উহারা একই সূণঝিল্লির মধ্যে আলাদা আলাদা ভূণে পরিণত হইয়া আলাদা আলাদা সন্তান জন্মে, কিন্তু ফুল থাকে একটি। সম যমজ সন্তানগণ হয়তো সকলেই পুত্র নচেৎ সকলেই কন্যা হইয়া থাকে। উহাদের দৈহিক গঠন ও মানসিক বৃত্তিসমূহে আশ্চর্য রকম মিল থাকে। একই ডিম্ব হইতে জন্মলাভ করে বলিয়া একই রকম যোগ্যতাসম্পন্ন হইয়া থাকে। শিল্প, সঙ্গীত, ধর্ম ইত্যাদির যে কোনো একটির প্রতি অনুরাগী হয় সকলে। উহাদের সকলের একই সময়ে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, একই রুচিসম্পন্ন হয় এবং হাতের লেখাও একই রকম হয়। কেহ কেহ বলেন যে, উহারা দূরে দূরে থাকিয়া একই রকম স্বপ্ন দেখে। তবে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে উহার কিছু ব্যতিক্রম হইতে পারে এবং কিছু কথার বাড়াবাড়িও হইতে পারে।
.
# বংশ প্রবাহে জীনের প্রভাব
জ্বীন-পরী –এই যুগল নামটি এদেশের আপামর জনসাধারণের কাছে অতি পরিচিত। কিন্তু উহাদের কাহারও সহিত আজ পর্যন্ত জনসাধারণের সাক্ষাতপরিচয় নাই। জ্বীন ও পরী সম্বন্ধে নানাবিধ কেচ্ছাকাহিনীর অন্ত নাই। জ্বীনগণ নাকি আগুনের তৈয়ারী অথচ অদৃশ্য, কিন্তু উহারা মানুষের মতোই এক ধরণের জীব। কোনো কোনো সময় কোনো কোনো জ্বীন নাকি মানুষের উপর বিশেষত মেয়েমানুষের উপর আশ্রয় করিয়া থাকে। উহাকে বলা হয় জ্বীনের দৃষ্টি। জ্বীনের আশ্রয় বা জ্বীনের দৃষ্টি যাহার উপর পতিত হয়, সে নাকি তাহার স্বকীয়তা হারাইয়া ফেলে এবং জ্বীনের মর্জিমাফিক কাজ করে। তথাকথিত জ্বীন ও তাহাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে এক শ্রেণীর মানুষের পুরাপুরি আস্থা থাকিলেও কোনো বিজ্ঞানী আজ পর্যন্ত ঐরূপ কোনো জ্বীনের অস্তিত্বের সন্ধান পান নাই। তবে তাহারা আর এক ধরণের জীনের সন্ধান পাইয়াছেন। সেই জীনেরাও অদৃশ্য, অথচ মানুষের দেহ-মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া থাকে।
সচরাচর দেখা যায় যে, জনক-জননীর সহিত ছেলে-মেয়েদের দৈহিক গঠন ও মানসিক বৃত্তিসমূহের কোনো না কোনো বিষয়ে কিছু না কিছু সাদৃশ্য থাকেই। জনক-জননীর দেহ হইতে জাতক উত্তরাধিকার সূত্রে যে সমস্ত গুণাগুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহার ধারক ও বাহক কি? এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, “ওসব ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা”। কিন্তু বিজ্ঞানীগণ বলেন অন্য কথা। তাহারা বলেন যে, উহার ধারক ও বাহক হইল জীন।
পূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে, জীবের জাতীয়তা নির্ভর করে তাহার দেহের জীবকোষের অভ্যন্তরস্থ ক্রোমোসোম-এর সংখ্যার উপর। বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, সেই ক্রোমোসোমগুলিও নিরেট বা শূন্যগর্ভ নহে, উহাদেরও গর্ভে আছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক প্রকার বিন্দু বিন্দু পদার্থ, যাহাদের অণুবীক্ষণেও দেখা যায় না। তাহারা এই জাতীয় অণুকণার নাম দিয়াছেন জীন (Gene)। তাহারা আরও বলেন যে, জনক-জননী তাহাদের ব্যক্তিত্বের যাহা কিছু জাতককে দান করে, এই জীনগণই তাহা বহন করিয়া আনিয়া থাকে। যেমন –চেহারা, চরিত্র, রুচি, অভিলাষ, কণ্ঠস্বর, বাচনভঙ্গি, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন কতিপয় শারীরিক ও মানসিক ব্যাধিও মাতা-পিতার নিকট হইতে সন্তান-সন্ততিরা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যথা –যক্ষ্মা, উপদংশ, উন্মাদ ইত্যাদি। ইহাদেরও ধারক ও বাহক হইল জীন। তবে পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে এবং অন্যান্য কতিপয় কারণে সব ক্ষেত্রে উহা প্রকট রূপ নেয় না।
.
# কৃত্রিম প্রজনন
মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তির সমষ্টিকেই বলা হয় ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্বের অনেক কিছুই লাভ করে মানুষ প্রকৃতি হইতে, জন্মের পর। যেমন –দৈহিক শক্তি অর্জনের জন্য নানাবিধ পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ এবং মানসিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য বিবিধ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বা সমাজের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ ইত্যাদি। এইভাবে যে সমস্ত শক্তি অর্জন করা হয়, তদ্বারা দেহযন্ত্র ও মনোবৃত্তিসমূহের পুষ্টি সাধিত হয় বটে, কিন্তু সৃষ্টি হয় না কিছুরই। ব্যক্তিত্বের মূল বিষয়বস্তু যাহা, তাহা অর্জিত নহে, জন্মগত বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত।
উত্তরাধিকার প্রাপ্তি কখনও অনিয়মিতভাবে হয় না। সভ্য মানব সমাজে বিশেষত মুসলিম জগতে উত্তরাধিকার বিষয়ক একটি পাকাপাকি বিধান রহিয়াছে, যাহাকে বলা হয় ফরায়েজ বিধান। দ্রুপ জীবজগতেও একটি উত্তরাধিকার বিধান রহিয়াছে। তবে পূর্বাবধি উহা ছিল মানুষের অজ্ঞাত। কিন্তু বর্তমানে জানা গিয়াছে উহার ধারা-উপধারা সবই।
পিতা তাহার সুযোগ্য পুত্রের হাতে সংসারের অনেক কাজ করিবার ক্ষমতা অর্পণ করিয়া থাকেন। অনুরূপ ভগবান তাহার নিজের করণীয় অনেক কাজ করিবার ক্ষমতাহবত মানে ছাড়িয়া দিয়াছেন বিজ্ঞানীদের হাতে। ইহার মধ্যে একটি কাজ হইল কৃত্রিম প্রজনন। এই কাজের জন্য ভগবান পথনির্দেশ দিলেন তাহার পুত্র (?) মেণ্ডেলকে ১৯ শতকের মধ্যভাগে।
মেণ্ডেল (Mendel) ছিলেন অস্ট্রিয়ার এক ক্ষুদ্র শহরের খ্রীস্টানী মঠের একজন পাদ্রী (খ্রীস্টানগণ বিশেষত পাদ্রীগণ ভগবানকে পিতা ও নিজেদেরকে তাহার পুত্র বলিয়া থাকেন)। তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, একই জাতের ফুল ও ফলের বীজ হইতে নানা ধরণের ফুল ও ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। যেমন– একটি লম্বা জাতের লাউয়ের বীজ হইতে লম্বা, গোল ও মাঝারি ধরণের লাউ জন্সিতে দেখা যায়, একটি আম্রবৃক্ষের বীজ হইতে বিভিন্ন ধরণের আম্রফল ফলিয়া থাকে, যাহাদের স্বাদ, গন্ধ ও বর্ণ হয় ভিন্ন ভিন্ন এবং কোনো মানুষও সর্ববিষয়ে তাহার মাতা ও পিতার অনুরূপ হয় না ইত্যাদি। তাই তিনি ভাবিতেছিলেন যে, প্রকৃতির এইসব খেয়ালিপনা কেন, এই সবের সাথে উহাদের যৌন প্রক্রিয়ার কোনো সম্পর্ক আছে কি না।
তিনি তাহার বাগানে কয়েকটি কড়াইশুটির গাছ লইয়া পরীক্ষা শুরু করিলেন। উহার কোনোটির লতা লম্বা, কোনোটির খাটো; কোনোটির খুঁটি পাকিলে হলুদ রং ধারণ করে, কোনোটি থাকে সবুজ; উহাদের ফুলের রংও ভিন্ন ভিন্ন। তিনি লম্বা জাতের সঙ্গে খাটো জাতের মিশ্রণ ঘটাইয়া প্রথম পরীক্ষা শুরু করিলেন এবং লম্বা জাতের ফুলের পরাগ লইয়া খাটো জাতের ফুলের বীজকোষে লাগাইয়া দিলেন। উহাতে যে ফল উৎপন্ন হইল এবং সেই ফল হইতে যে বীজ জন্সিল, তাহা বপন করিয়া দেখিলেন যে, পরের (দ্বিতীয়) বৎসর সকল চারাই হইল লম্বা জাতের। ইহাদের বীজ পুনঃ বপন করিলে তৃতীয় বৎসরে দেখা গেল যে, উহাদের ৩/৪ ভাগ লম্বা ও ১/৪ ভাগ খাটো গাছ জন্মিল। চতুর্থ বৎসরে উহাদের বীজ পুনঃ বপন করিলে দেখা গেল যে, খাটো গাছের বীজ হইতে শুধু খাটো গাছই জমিল, কিন্তু লম্বা গাছের বীজ হইতে জন্মিল পুনরায় তিন ভাগ লম্বা ও এক ভাগ খাটো। অতঃপর তিনি কড়াইশুটির অন্যান্য গুণ যথা –শুটির রং, ফুলের রং ইত্যাদি লইয়া পরীক্ষা করিয়াও ফল পাইলেন ঠিক একই রকম। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, জীবের গুণগত বৈচিত্রগুলি সবই যৌনঘটিত ব্যাপার।
মেণ্ডেল সাহেবের পথ অনুসরণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কালো বর্ণের গাভীর সহিত কালো বর্ণের ষাঁড়ের মিলন ঘটাইলে সবগুলি বাচ্চাই কালো বর্ণের হইয়া থাকে এবং কালো বর্ণের গাভীর সহিত শাদা বা অন্য কোনো বর্ণের ষাঁড়ের মিলনের ফলে জন্মে দোআঁশলা বাছুর। লাল, কালো ও শাদা বর্ণের গাভীর সহিত লাল, কালো ও শাদা বর্ণের ষাঁড়ের মিলন ঘটাইলে তাহার ফল দাঁড়ায় এইরূপ —
লাল ষাঁড় কালো ষাঁড় শাদা ষাঁড়
লাল গাভীর বাছুর= লা২ লা-কা লা-শা
কালো গাভীর বাছুর = কা-লা কা২ কা-শা
শাদা গাভীর বাছুর = শা-লা শা-কা শা২*
[* প্রাণতত্ত্ব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ১১৬।]
উপরোক্ত হিসাবে দেখা যায় যে, নয়টি বাছুরের মধ্যে লা২, কা২, শা২ –এই তিনটি বাছুর তাহাদের মাতা ও পিতার নিকট হইতে একই বর্ণ (গুণ) প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া উহারা একই বর্ণ লাভ করিয়াছে এবং অবশিষ্ট ছয়টি দুই বর্ণ লাভ করিয়াছে বলিয়া হইয়াছে দোআঁশলা।
মানুষের উপরেও মেণ্ডেলিয়ান বংশানুক্রমের নিয়ম সমভাবে প্রযোজ্য। ও বাবা উভয়ের যদি কটা চক্ষু থাকে, তাহা হইলে তাহাদের সব ছেলে-মেয়ের কটা চক্ষু হইবে। কিন্তু মা-বাবার যদি কালো চক্ষু থাকে, তবে অধিকাংশ ছেলে-মেয়ের কালো চক্ষু হইলেও কৃচিৎ কটা চক্ষুও হইতে পারে। এইখানে চক্ষু ও চুল সম্বন্ধে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া গেল–
চোখ ও চুলের বৈশিষ্ট অনুসারে মানুষের বংশানুক্রম
জনক জননী সন্তান।
১. কালো চোখ কোঁকড়া চুল x কালো চোখ কোঁকড়া চুল = সব ঐ অথবা ১/৪ কটা চোখ;
১/৪ সোজা চুল।
২. ,, ,, x ,, সোজা চুল = সব কালো চোখ (১/৪ কটাও হইতে পারে);
সব কিংবা অর্ধেক সোজা চুল।
৩. ,, সোজা চুল x ,, ,, = সব কালো চোখ (১/৪ কটাও হইতে পারে);
সব সোজা চুল।
৪. কালো চোখ কোঁকড়া চুল x কটা চোখ কোঁকড়া চুল = সব কিংবা অর্ধেক কালো চোখ; সব
কিংবা ৩/৪ কোঁকড়া চুল। ৫. ,, ,, x ,, সোজা চুল = সব কিংবা অর্ধেক কালো চোখ; সব
কিংবা অর্ধেক কোঁকড়া চুল
৬. ,, সোজা চুল x ,, ,, = সব কিংবা অর্ধেক কালো চোখ; সব
সোজা চুল।
৭. কটা চোখ কোঁকড়া চুল x ,, কোঁকড়া চুল = সব কটা চোখ; সব কিংবা ৩/৪ কোঁকড়া চুল।
৮. ,, ,, x ,, সোজা চুল = সব কটা চোখ; সব কিংবা ১/২ কোঁকড়া চুল।
৯. ,, সোজা চুল x ,, ,, = সব কটা চোখ; সব সোজা চুল।*
[* প্রাণতত্ত্ব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ১২৩।]
সাম্প্রতিক কালের জীব ও উদ্ভিদ বিজ্ঞানীগণ মেণ্ডেলিজমের ভিত্তিতে গবেষণা চালাইয়া বংশানুক্রম সম্বন্ধে এক নূতন যুগের সূচনা করিয়াছেন। অণুবীক্ষণাদি যন্ত্রের যতই উন্নতি সাধিত হইতেছে, বিজ্ঞানীগণ ততই ক্রোমোসোমের অভ্যন্তরস্থ সূক্ষাতিসূক্ষ্ম অণু-কণা সম্বন্ধে নব নব তত্ত্ব অবগত হইতেছেন। মেণ্ডেল সাহেব না জানিলেও আধুনিক বিজ্ঞানীগণ জানিতে পারিয়াছেন যে, জীবের বংশানুক্রমে যে কোনোও গুণের জন্য জীনগণই দায়ী। তাই বিজ্ঞানীগণ নানা উপায়ে জীনগণের অবস্থান্তর ঘটাইয়া ঈঙ্গিত গুণসমূহের উৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট হইয়াছেন এবং উহাতে তাহারা সাফল্য অর্জন করিয়াছেন যথেষ্ট।
মনে হয় যে, কৃত্রিম প্রজননে সবচেয়ে বেশি উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে উদ্ভিদ বিশেষত কৃষিবিজ্ঞানে। প্রতি বৎসর নূতন নূতন ধরণের বহু জাতের ফুল-ফলের গাছ উৎপন্ন করিয়া আমাদের উপহার দিতেছেন নার্সারিওয়ালারা। ধান, পাট, আখ, গম ইত্যাদি ফসল, লাউ, কুমড়া ইত্যাদি তরিতরকারি এবং আম, কাঁঠাল, কলা, নারিকেল ইত্যাদি যে সকল উন্নত মানের গাছ গাছড়া এযাবত উদ্ভিদবিজ্ঞানীগণ কৃত্রিম প্রজনন দ্বারা উৎপন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কৃষকগণ তাহার যথাযথ ব্যবহার করিলে দেশের খাদ্যাভাব ও অর্থাভাব দূর হইবে, এইরূপ আশা করা যায়।
কৃত্রিম প্রজননের ফলে গৃহপালিত পশু-পাখিদেরও উৎকর্য হইয়াছে ও হইতেছে প্রচুর। ঐসমস্তের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় হাঁস-মোরগ ও গবাদি পশুর সর্বাধুনিক খামারগুলি দর্শনে। এখন বিজ্ঞানীগণ কৃত্রিম প্রজননের অভিযান চালাইতেছেন মৎস্যরাজ্যেও এবং সেখান হইতেও কানে আসিতেছে তাহাদের বিজয়ডঙ্কার শব্দ।
কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে মানুষের কৌলিক ব্যাধি ও অন্যান্য দোষ-ত্রুটি সংশোধনপূর্বক কি রকম মনুষ্য সমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হইতে পারে, সেই বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য বিজ্ঞানের একটি নূতন শাখার সৃষ্টি হইয়াছে, যাহার নাম সুজননবিদ্যা (Eugenics)।
.
# জন্মশাসন
জগতের সব কিছুই পরিবর্তনশীল, এমনকি স্বয়ং জগতটিও তদ্রূপ। তবুও একশ্রেণীর মানুষ। “বিধাতার বিধান অপরিবর্তনীয়” –ইহা বলিয়া জগতের বহু বিষয়কে অপরিবর্তনীয় রূপে ধরিয়া রাখিতে সতত চেষ্টা করে। কিন্তু বিধাতার (প্রকৃতির) বিধানবশতই তাহা অসম্ভব হইয়া পড়ে। বিধাতার অনেক আশীর্বাদ বর্তমানে অভিশাপে পরিণত হইয়াছে। উহার মধ্যে একটি হইল মানুষের বংশবৃদ্ধি।
বংশবৃদ্ধি অর্থাৎ সন্তান-সন্ততি হওয়া নাকি বিধাতার একটি মস্ত বড় আশীর্বাদ। পূর্বে বলা হইত এবং এখনও কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, যে ব্যক্তির সন্তান-সন্ততির সংখ্যা যত অধিক, সে তত অধিক আশীর্বাদপ্রাপ্ত অর্থাৎ ভাগ্যবান। বিধাতার আশীর্বাদের ফলেই নাকি রাবণের লক্ষ পুত্র, ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র এবং হজরত আদমের পুত্রকন্যার সংখ্যা নাকি একশত বিশ। যদিও এই যুগে ঐরূপ ঢালাও আশীর্বাদ পৃথিবীর কোথায়ও দেখা যায় না, তথাপি এক দম্পতির দশ-বিশটি সন্তান প্রাপ্তির আশীর্বাদ বিরল নহে। পূর্বে মানুষের বহু সন্তান কাম্যও ছিল। কোনো নববধূকে আশীর্বাদ করিয়া বলা হইত, “তুমি সাত পুতের মা হও”। আর আজ? এক জোড়ার অধিক সন্তান কাহারও কাম্য নহে।
উপরোক্ত আশীর্বাদের ফলে বর্তমানে জগতে ঘটিয়াছে খাদ্যের অভাব ও ঘটিতেছে অনাহারে মানুষের মৃত্যু। আমাদের এই সোনার বাংলাদেশে অনাহারে যাহারা মারা গিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা হয়তো হাজার হাজার। কিন্তু তিলে তিলে মৃতের সংখ্যা লক্ষ লক্ষও নহে, কোটি কোটি।
বহু সন্তানের আশীর্বাদের কবল হইতে মানব জাতিকে উদ্ধার করিবার মানসে বর্তমান জগতের জননায়কগণ অধুনা প্রবর্তন করিয়াছেন জন্মশাসন, যাহার প্রচলিত নাম হইল পরিবার পরিকল্পনা বা জন্মনিয়ন্ত্রণ। আর রাষ্ট্রনেতাগণ এই কাজটি সাফল্যমণ্ডিত করিবার ভার অর্পণ করিয়াছেন জীববিজ্ঞানীদের উপর।
বর্তমান জগতের কোনো বিবেকবান ব্যক্তিই জন্ম, মৃত্যু, খাদ্য, সম্পদ ইত্যাদি বিষয়ের দায়-দায়িত্ব বিধাতার মাথায় চাপাইয়া দিয়া নিজে আরামে বসিয়া থাকিতে ইচ্ছুক নহেন। বিশেষত বিজ্ঞানীগণই ইহাতে অগ্রগামী। যদিও পরিবার পরিকল্পনা আন্দোলনের বয়স খুবই অল্প, তথাপি বিজ্ঞানীগণ জন্মনিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে নানাবিধ গবেষণা চালাইয়া উহার জন্য অনেকগুলি উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন এবং উহা অবলম্বনে আশানুরূপ ফললাভ হইতেছে।
জন্মনিয়ন্ত্রণ যৌনক্রিয়ানিয়ন্ত্রণ নহে; উহা হইল নারী-পুরুষের সন্তানোৎপাদিকা শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা। নারী ও পুরুষের মিলনের ফলেই সন্তানোৎপাদিত হয় না, উহা হয় শুক্রকীট ও ডিম্বকোষের মিলনের ফলে। তাই নারী ও পুরুষের মিলন অব্যাহত রাখিয়া শুধু শুক্রকীট ও ডিম্বকোষের মিলন ব্যাহত করাই জন্মনিয়ন্ত্রণের মুখ্য প্রক্রিয়া। আর এই কাজের জন্য প্রধানত দুইটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়া থাকে। প্রথম পদ্ধতি হইল রতিকালে নানা কৌশলে শুক্রকীট ও ডিম্বকোষের মিলনে বাধাদান করা এবং দ্বিতীয় পদ্ধতি হইল নারী ও পুরুষের ডিম্বাধার ও শুক্ৰাধারে ডিম্বকোষ ও শুক্রকীট জন্মিতে না দেওয়া। আর যদি ইহার একটিও কার্যকর না করা যায়, তবে চরম পদ্ধতি হইল ভূণ নষ্ট করা। কিন্তু ইহা অনভিপ্রেত। প্রথমোক্ত পদ্ধতি দুইটি অনুসারে বিজ্ঞানীগণ এযাবত বহু কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাহার মধ্যে এইখানে কয়েকটি কৌশলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।
১. পিচকারি বা ডুশ প্রয়োগ –রতিক্রিয়ার অব্যবহিত পরেই শুধু জল অথবা সাবান-জল, কুইনাইনের জল, রজার্স পাউডারের জল, লেবুর রস বা ভিনিগার মিশ্রিত জলের পিচকারি বা ডুশ প্রয়োগে স্ত্রীঅঙ্গ ধৌত করিলে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু পুরুষের রেতপাতের সঙ্গে সঙ্গে যদি উহা জরায়ুতে প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে এই পদ্ধতি কার্যকর নাও হইতে পারে। ডুশের বহুবিধ প্রয়োগরূপ আছে।
২. স্পঞ্জ –দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় প্রায় তিন ইঞ্চি একখানা ভালো নরম স্পঞ্জ সংগ্রহ করিয়া রতিক্রিয়ার পূর্বে উহা ঠাণ্ডা জলে, সাবান-জলে, ফিটকিরি ভিজানো জলে অথবা ঝাজবিহীন তৈলে ভিজাইয়া অল্প নিংড়াইয়া স্ত্রীঅঙ্গের মধ্যে দিয়া, অশুলির সাহায্যে ঠাসিয়া জরায়ুমুখে স্থাপন করিয়া লইতে হয়। এই পদ্ধতি রক্ষা করিয়া কার্য করিলে জন্মরোধ হইয়া থাকে। কিন্তু কার্যকালে স্পঞ্জ জরায়ুমুখ হইতে সরিয়া গেলে গর্ভসঞ্চারের সম্ভাবনা থাকে।
৩. কুইনাইন পেসারি –কুইনাইন পেসারি নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র ও গোলাকার বটিকা বাজারে পাওয়া যায়। ইহা কুইনাইন, কোকো প্রভৃতির সংযোগে প্রস্তুত হয়। এই পেসারি মিলনের ১০-১৫ মিনিট পূর্বে শ্রীঅঙ্গে প্রবেশ করাইয়া দিলে উহা গলিয়া যায়। অতঃপর মিলনের ফলে গর্ভসঞ্চার হয় না। কেননা, এই ঔষধটির গুণে শুক্রকীটসমূহ মরিয়া যায়। কিন্তু ঔষধ শক্তিশালী না হইলে অথবা কার্যকালের পূর্বে বটিকা না গলিয়া থাকিলে গর্ভসঞ্চারের আশকা থাকে। বাজারে বহুবিধ পেসারি বাহির হইয়াছে।
৪. জেলি, ক্রীম বা পেস্ট –জেলি, ক্রীম বা পেস্ট বাজারে পাওয়া যায়। ইহা শুক্রকীটম্বংসী মাল-মশলায় তৈয়ারী। ইহার যে কোনো একটি রতিক্রিয়ার পূর্বে উভয়ের জননেন্দ্রিয়ে ব্যবহার করিলে উভয়ের অঙ্গ সঞ্চালনেই স্ত্রীঅঙ্গে প্রক্ষিপ্ত হইয়া যায় এবং উহার সংস্পর্শে শুক্রকীটসমূহ মারা যায়। ফলে গর্ভধারণ ব্যাহত হয়।
৫. কনডম— ইহা একমাত্র পুরুষের ব্যবহারোপযোগী পুরুষাঙ্গের এক প্রকার আবরণী বা খাপবিশেষ। কনডম সাধারণত পাতলা রাবার বা প্লাস্টিকের তৈয়ারী। ইহার একদিক খোলা এবং অপরদিক বন্ধ। এই দেশে ইহা ‘ফ্রেঞ্চ ক্যাপ’ বা শুধু ‘ক্যাপ’ নামেই বহুল প্রচলিত।
মৈথুনের পূর্বে পুরুষাঙ্গে মোজার মতো কনডম পরিধান করিতে হয়। ইহাতে কার্যকালে যে বীর্যপাত হয়, তাহা শ্ৰীঅঙ্গে পতিত না হইয়া কনডমের ভিতরেই থাকিয়া যায়। ইহার ফলে গর্ভসঞ্চার হয় না। বর্তমানে বহুবিধ কনডম বাজারে পাওয়া যায়।
৬. পেসারি –ইহা স্ত্রীলোকের ব্যবহারের জন্য রাবার বা প্লাস্টিক নির্মিত আবরণী। ইহা বিভিন্ন আকৃতির হইয়া থাকে। পেসারিগুলির যে কোনও একটি নারীর জরায়ুমুখে পরাইয়া দিলে উহা জরায়ুগ্রীবায় আঁট হইয়া লাগিয়া থাকে। জরায়ুগ্রীবায় পেসারি চাপিয়া জরায়ুমুখ একেবারে আবৃত থাকে। কাজেই পুরুষের বীর্য জরায়ুতে প্রবেশ করিতে পারে না। ফলে গর্ভসঞ্চার হইতে পারে না। অধুনা বহুবিধ পেসারির প্রচলন হইয়াছে।
৭. শুক্ৰবাহী নালী কর্তন— বন্ধ্যাকরণের উত্তম পন্থা অস্ত্রোপচার। পুরুষের বেলায় অণ্ডকোষের সামান্য চিরিয়া শুক্রবাহী নালিকায় দুই প্রান্তে বাধিয়া ও মধ্যভাগ হইতে এক ইঞ্চি পরিমাণ কাটিয়া ঐ স্থানটি পুরাইয়া দেওয়া হয়। ভালোভাবে অস্ত্রোপচার হইলে ইহাতে পুরুষের যৌন আসক্তি বা আনন্দভভাগে কোনোই বাধা হয় না। সাধারণের মতোই সহবাসে তাহার শুক্রশ্মলন হয়, তবে পরিমাণে কম। কিন্তু উহাতে শুক্রকীট থাকে না বলিয়া গর্ভসঞ্চার হয় না। যদিও ইহা স্থায়ী বন্ধ্যাকরণ, তবে অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ পুনঃ অস্ত্রোপচার করিয়া শুক্ৰবাহী নালী জোড়া দিয়া বন্ধ্যাত্ব দূর করিতে পারেন।
৮. শুক্রকোষ দূরীকরণ– শুক্রকোষ দূরীকরণ একটি চরম পন্থা। উহাতে দুইটি কোষই বাহির করিয়া ফেলা হয় এবং তজ্জন্য শরীর, মন ও যৌন স্বাস্থ্যের প্রভূত ক্ষতি হইয়া থাকে। পুরুষ দেহে ও মনে মেয়েলি ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। ইহাতে আর কখনও সন্তানোৎপাদন ক্ষমতা ফিরিয়া আসে না।
৯. ফ্যালোপিয়ান নল কর্তন –ইহাতে ফ্যালোপিয়ান নল বা ডিম্ববাহী নালী কাটিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হয়। উহাদিগকে একেবারে ফেলিয়াও দেওয়া যায়। ইহাতে ডিম্বাশয় হইতে। ডিম্বকোষ জরায়ুতে আসিতে না পারায় নারী বন্ধ্যাত্বপ্রাপ্ত হয়। সর্বোৎকৃষ্ট পথ হইল, ঐ নল দুইটির ডিম্বাশয়ের দিকের প্রান্ত দুইটিকে তলপেটের প্রাচীরে প্রোথিত করিয়া দেওয়া। শেষোক্ত প্রক্রিয়ায় আবার দরকার হইলে অনেক ক্ষেত্রে সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতা ফিরাইয়াও আনা যায়। এইরূপ বন্ধ্যাকরণে স্ত্রীর স্বাভাবিক যৌন আসক্তি ও আনন্দভোগে কোনো গোলযোগ উপস্থিত হয় না। মাসিক স্রাবেও কোনো গোলযোগ ঘটে না।
১০. ডিম্বাশয় দূরীকরণ –নারীর ডিম্বাশয় দুইটি কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া উহাকে চিরবন্ধ্যা করা যায় বটে, কিন্তু তাহার পরিণাম খারাপ হইয়া থাকে। ফলে পুরুষের শুক্রকোষ দূরীকরণের মতো নারীর শরীর ও মনের মেয়েলি ভাব কমিয়া যায় ও পুরুষালি ভাব আসিতে পারে।* [*জন্মনিয়ন্ত্রণ, আবুল হাসানাৎ, পূ, ৮৩-১২৫।]
উপরোক্ত পদ্ধতিসমূহ ছাড়া জন্মরোধের আর একটি পদ্ধতি হইল ঔষধ ব্যবহার করা। বর্তমানে এইরূপ কতগুলি ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে, যাহা সেবনে রমণীদের ডিম্বাশয়ে ডিম্বকোষ জন্মে না, অথবা জন্মিলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। ফলে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে সন্তানোৎপত্তি রহিত হয়।
অনভিপ্রেত হইলেও জন্মশাসনের চরম পদ্ধতি হিসাবে গর্ভপাত ঘটাইবার পদ্ধতিটি বহুদিন হইতে প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে প্রায় সব দেশেই প্রচলিত আছে। ইহাতে এইরূপ কোনো ঔষধ গর্ভিনীকে সেবন করানো বা জরায়ুমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়, যাহার ফলে ভূণ নষ্ট হয় বা সন্তান মারা যায় এবং জরায়ুর উত্তেজনা বা সঙ্কোচনের দরুন গর্ভপাত হয়। কিন্তু এই সমস্ত প্রক্রিয়ায় সব ক্ষেত্রেই বিপদের আশঙ্কা থাকে, এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে আশঙ্কা থাকে গর্ভিনীর প্রাণহানিরও।
আমাদের দেশের বর্তমান সরকার পরিবার পরিকল্পনা বনাম জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন এবং এই ব্যাপারে সর্বাত্মক সাফল্য লাভের জন্য দেশের প্রায় সর্বত্র উহার যথাবিহিত ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে ও হইতেছে। আশা করি বিধাতা বর্তমান দুনিয়ার মানুষের দুই সন্তান’-এর প্রার্থনা অচিরেই মঞ্জুর করিবেন।
————
[২৭. প্রাণতত্ত্ব, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পৃ. ১০৭, ১০৮।
২৮. ঐতিহাসিক অভিধান, মো. মতিয়র রহমান, পৃ. ২৩, ২৪।]
১২. সভ্যতার বিকাশ
সভ্যতার বিকাশ
# হাতিয়ারের ক্রমোন্নতি
মানব জাতির ক্রমোন্নতির মূলে রহিয়াছে হাতিয়ারের ক্রমোন্নতি। আদিম মানবের জীবনে একটিমাত্র সমস্যা ছিল, তাহা হইল আত্মরক্ষা। সুখেই হউক আর দুঃখেই হউক, বাঁচিয়া থাকাই ছিল তাহাদের প্রধান সমস্যা। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে প্রথমত চাই খাদ্য ও শত্রুর কবল হইতে মুক্তি। খাদ্যসংস্থানে ঝামেলা থাকিলেও উহা তত মারাত্মক নহে। কেননা, বনে বনে ঘুরিয়া ফলমূল সংগ্রহ বা ছোট ছোট জানোয়ার হত্যা করিয়া তাহার কাঁচা মাংস ভক্ষণ করা একেবারে অসাধ্য ছিল না। হয়তো দুই-এক বেলা অনাহারে থাকিলেও তাহাতে মৃত্যুভয় নাই। শীতাতপ হইতে রক্ষা পাইতে হইলে কোনো রকমে কায়ক্লেশে গাছের কোটরে বা পাহাড়ের গুহায়। প্রবেশ করিতে পারিলেই ব্যাস। কিন্তু বাঘ-ভালুকাদি হিংস্র জানোয়ারের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়াই ছিল কঠিন কাজ। শত্রুর কবল হইতে আত্মরক্ষার উপযোগী কোনো ব্যবস্থাই ছিল না মানুষের গায়ে, যেরূপ ছিল পশু-পাখিদের। বাঘের মতো বিরাট দেহ বা দাঁত-নখরও ছিল না, আর গরু-মহিষের মতো শিংও ছিল না। সম্বল ছিল মাত্র দুইখানা হাত। তাহাও বেশি বড় নহে এবং উহাতে শক্তিই বা কতটুকু! তাই আদিম মানব সাহায্য লইল হাতিয়ারের। সেই হাতিয়ার আর কিছুই নহে –গাছের ডাল ও পাথরের টুকরা।
বন্য জানোয়ারের আক্রমণ সাধারণত আঁচড়ানো ও কামড়ানো। কিন্তু একেবারে গায়ে পড়া শত্রু না হইলে এ ধরণের আক্রমণ চলে না। আদিম মানবেরা যখন দৃঢ় মুষ্টিতে গাছের ডাল ধরিয়া দলবদ্ধভাবে আক্রমণ চালাইত, তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জানোয়ার মারা পড়িয়া উহাদের খাবার তো জোগাড় হইতই, বরং অনেক হিংস্র জন্তু লড়াইয়ে হার মানিত। কেননা, ইহাতে আক্রমণকারীরা থাকিয়া যাইত হিংস্র জন্তুদের নাগালের বাহিরে।
আদিম মানব শিকার ও আত্মরক্ষার কাজে প্রধানত গাছের ডাল বা লাঠিই ব্যবহার করিত। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সাথে সাথে যখন বুঝা গেল যে, কঠিন কোনো কিছু খুঁড়িয়া মারিলে আরও দূর হইতে আক্রমণ চালানো যায়, তখন উহারা ঐ কাজে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল পাথরের টুকরা –যে রূপে পাওয়া যাইত সেই রূপেই। যখন দেখা গেল যে, পাথরের টুকরাগুলি ধারালো সূঁচালো হইলে শত্রুকে ঘায়েল করা যায় আরও সহজে, তখন উহারই চেষ্টা চলিতে লাগিল। এইভাবে কালক্রমে সৃষ্টি হইল আদিম মানবদের নানা ধরণের পাথরের হাতিয়ারের।
ক্রমে দেখা গেল যে, ঘুড়িয়া মারা হাতিয়ার সব সময়ে লক্ষ্যস্থলে পড়ে না। তাই অনেক সময়েই শিকার ফসকাইয়া যায়। চেষ্টা চলিল অব্যর্থ আঘাত হানিবার হাতিয়ার তৈয়ারের। একখণ্ড কাঠের দণ্ডে পাথরের ফলা যুক্ত করিয়া তৈয়ার করা হইল বর্শা, বল্লম, ক্রমে উড়ন্ত বর্শা।
উড়ন্ত বর্শাও হাতে ছোঁড়া হইত। কাজেই উহার গতিবেগ ও পাল্লা তত বেশি নহে। উড়ন্ত বর্শাই ক্রমে রূপ পাইল তীর-ধনুকের। মানব সভ্যতার এক বিরাট সাফল্য এই তীর-ধনুকের আবিষ্কার। আদিতে ইহার ব্যবহার ছিল পশু-পাখি শিকার ও আত্মরক্ষামূলক কাজেই এবং উহার ব্যবহার চলিয়াছিল হাজার হাজার বৎসর। সভ্যতাবৃদ্ধির সাথে সাথে তাম্র ও লৌহ আবিষ্কারের পর তীর-ধনুকের উন্নতি হইয়াছিল অসাধারণ। কিন্তু উন্নতি হইলে কি হইবে, উহা দ্বারা পশু পাখি হত্যার বদলে আরম্ভ হইয়াছিল নরহত্যা এবং পশু-পাখির স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিল রামানুজ লক্ষ্মণ, লঙ্কেশ্বর রাবণ ও নূরনবীর দৌহিত্র ইমাম হোসেনও।
আধুনিক যুগে আবার তীর-ধনুকের চেহারা বদল হইয়া উহার তীরটি হইয়াছে গোল এবং ধনুটি হইয়াছে সোজা –সৃষ্টি হইয়াছে বন্দুক, কামান ইত্যাদি মারণাস্ত্রের। শেষমেশ পারমাণবিক বোমা।
হাতিয়ার শুধু মারণাস্ত্রই নহে। যাহা হাতের বদলে ব্যবহৃত হয় বা হাতের শক্তি বাড়াইয়া দেয়, তাহাই হাতিয়ার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। মানুষের সমাজ জীবনে, বিশেষত শিল্প, কৃষি, চিকিৎসা বিজ্ঞান ইত্যাদিতে রকমারি হাতিয়ার বনাম কল কারখানার অন্ত নাই। অধুনা মানব সভ্যতার মাপকাঠিই হইল হাতিয়ার। যে জাতির হাতিয়ার যত উন্নত, সেই জাতি সভ্যতায় তত অগ্রগামী।
.
# জাতিগত জীবন ও ব্যক্তিজীবনে সাদৃশ্য
বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, ক্রমবিবর্তনের নিয়ম মতে মানুষ তাহার জাতিগত জীবনে যে যে অবস্থাপ্রাপ্ত হইয়া বর্তমান অবস্থায় পৌঁছিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি অবস্থা মূর্ত হইয়া উঠে তাহার ব্যক্তিজীবনে। মনুষ্য জাতির বিবর্তনের প্রধান প্রধান স্তর বা অবস্থা হইল –১. মৎস্য, ২. সরীসৃপ, ৩. পশু, ৪. অর্ধমানব, ৫. অসভ্য মানব ও ৬. সভ্য মানব ইত্যাদি। মানব সভ্যতার আবার কয়েকটি সুস্পষ্ট ধাপ আছে। যথা –পুরাতন পাথর যুগ, নূতন পাথর যুগ, তাম্র যুগ, লৌহ যুগ ইত্যাদি। ইহাকে আমরা বলিতে পারি মানব সভ্যতার –শৈশব, বাল্য, কৈশোর ও যৌবন অবস্থা। এই সমস্ত অবস্থা মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে কি রকম প্রতিফলিত হইতেছে, এইখানে আমরা তাহার কিছু আলোচনা করিব।
মৎস্য অবস্থা
মানুষের দৈহিক রূপের বিকাশ শুরু হয় এই মৎস্য অবস্থায়। মাছের মতো জলজীবন, মাছের মতো চেহারা এবং বহির্জগতের আলো-বাতাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকে না মাছের মতোই। ইহা ব্যক্তিজীবনের প্রাথমিক অবস্থা, ইহার নাম শুক্রকীট।
সরীসৃপ অবস্থা
পশুদের মতো সরীসৃপরাও চারি পায়ের অধিকারী বটে, কিন্তু উহারা পায়ের দ্বারা পেট শূন্যে তুলিয়া রাখিতে পারে না, মাটিতে টানিয়া চলে। মানবশিশুরাও ৫-৬ মাস বয়স্ক হইলে উপুড় হইতে শুরু করে এবং ক্রমে কুমিরাদি সরীসৃপদের ন্যায় মাটিতে বুক টানিয়া চলিতে থাকে। এই অবস্থাকে বলা হয় শিশুর বুকে চলা বা বুকে হাঁটা।
পশু অবস্থা
পশুরা চারি পায়ে হাঁটে। বিজ্ঞানীদের মতে, মানুষও কোনো এক সময়ে পশু পর্যায়ে ছিল এবং চারি পায়ে হাঁটিত। ঐ অবস্থাটি ব্যক্তিজীবনে প্রতিফলিত হয় শৈশবে। ন্যূনাধিক ৯-১০ মাস বয়স্ক শিশুরা হামাগুড়ি দিয়া চলিতে আরম্ভ করে। ইহাতে শিশুরা চলিবার জন্য হাত ও পা সমানে ব্যবহার করে পশুদের মতোই।
অর্ধমানব অবস্থা
মানুষের পূর্বপুরুষেরা পুরাপুরি দ্বিপদ হইবার আগে গরিলা, শিম্পাঞ্জি ও বানরাদির ন্যায় কখনও দুই পায়ে এবং কখনও চারি পায়ে হাঁটিত এবং চলিবার সময় দেহ সামনের দিকে ঝুঁকিয়া থাকিত। সদ্য হাঁটিতে শেখা শিশুরাও ঐরূপ কখনও হাঁটে, আবার কখনও হামাগুড়ি দেয় এবং ঐ অবস্থায় কোনো শিশুই সোজা হইয়া হুঁটিতে পারে না।
অসভ্য অবস্থা
মানুষ যখন পুরাপুরি দ্বিপদ জীব অর্থাৎ মানুষ নামের অধিকারী হইয়াছিল, তখন তাহারা ছিল বুনো বা অসভ্য মানুষ। তখন তাহারা খাইবার মতো যাহা পাইত, তাহা দিয়াই উদর পুরাইত; ক্ষুধানিবৃত্তিই ছিল খাইবার উদ্দেশ্য। তাহারা উলঙ্গ থাকিত, বনে বনে ঘুরিয়া পশু-পাখি মারিত ও উহা কাঁচা ভক্ষণ করিত। বৃক্ষকোটরে বা পর্বতগুহায় বাস করিত। তুচ্ছ বিষয় লইয়া কলহ করিত, আবার পরমুহূর্তে উহা ভুলিয়া যাইত। তাহারা ছিল অকপট, নিরলস, স্বেচ্ছাচারী ও নোংরা। বলা। বাহুল্য, ঐরূপ অসভ্য বা অনুন্নত মানবগোষ্ঠী আজিও দুনিয়ার কোনো কোনো অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।
মানবশিশুদের মধ্যে উক্তরূপে এমন একটি অবস্থা আসিয়া থাকে, যখন তাহারা সাধারণত খাদ্যাখাদ্য যাহা হাতের কাছে পায়, তাহাই তুলিয়া মুখে দেয়, মাতা-পিতার সঙ্গেও ‘তুই’ শব্দটি ব্যবহার করে, ধুলা-বালি লইয়া খেলিতে ও ময়লা গায়ে থাকিতে চায়, উলঙ্গ থাকিতে লজ্জাবোধ করে না ইত্যাদি অসভ্যজনোচিত আচরণ করিয়া থাকে। অসভ্যদের মতোই শিশুরা অকপট, সত্যবাদী, নিরলস, নোংরা এবং স্বেচ্ছাচারী হইয়া থাকে। শিশুদের তুচ্ছ বিষয় লইয়া সাথীদের সাথে বকাবকি, মারামারি, আবার নিমেষে মিলিয়া-মিশিয়া খেলা করা, ঢিল ছোঁড়া, পাখি ধরা, গাছে উঠা ইত্যাদির প্রবণতা সেই আদিম অসভ্য মানবদের চরিত্রেরই ছায়া।
সভ্য অবস্থা
মানব সভ্যতার প্রধানত চারিটি ধাপ। যথা –শৈশব, বাল্য, কৈশোর ও যৌবনাবস্থা।
সভ্যতার শৈশবাবস্থা –সভ্য জগত ও অসভ্য জগতের মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নাই। সভ্যতা আসিয়াছে যুগ যুগ ধরিয়া, হাজার হাজার বৎসরে, ক্রমে ক্রমে। কিন্তু আজিও কি আমাদের সমাজে পূর্ণ সভ্যতা আসিয়াছে? আজিও সভ্যতার দাবিদারদের সমাজে রমণীদের অগচ্ছেদনপূর্বক অলকার পরানো, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি, মহামারী ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিবারণের জন্য দেবতাদের কাছে ধর্ণা দেওয়া ইত্যাদি যে সকল রীতি-নীতি প্রচলিত আছে, (প্রিয় পাঠক রাগ করিবেন না) ঐগুলি সবই অসভ্য যুগের প্রথা। পক্ষান্তরে সভ্যজনোচিত কোনো কোনো প্রথা অসভ্য যুগেও ছিল। যেমন –মাতা-পিতা বা বংশপ্রধানকে মান্য করা ইত্যাদি।
শেষোক্ত নীতিটির উপর ভিত্তি করিয়াই অসভ্য মানব যুগে যুগে পা বাড়াইয়াছিল সভ্যতার দিকে। পিতৃপ্রধান হইতে উদ্ভব হইয়াছে গোষ্ঠীপ্রধানের যুগ, অতঃপর সমাজপতি বা মোড়ল প্রধানের যুগ ও পরে রাষ্ট্রপ্রধান বা রাজা-বাদশাহের যুগ। সে যাহা হউক, মানব সভ্যতার শৈশবে পিতৃপ্রধান যুগই ছিল। সন্তানেরা মাতা-পিতার আহার-বিহার, চাল-চলন অনুসরণ করিত; তাহাদের যে কোনো বাক্য অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিত। বস্তুত পিতা-মাতাই ছিল সেকালের মানুষের শিক্ষাগুরু।
মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে ঐ অবস্থাটি প্রতিফলিত হয় তিন-চারি বৎসর বয়সে। অধিকাংশ শিশুরই এই বয়সের সকল কথা বা ঘটনা স্মরণ থাকে না, কিন্তু নিজ্ঞান মনে (Unconscious Mind) উহার দাগ থাকে। মনোবিজ্ঞানীগণ বলেন যে, শিশুদের ভাবী জীবনে চরিত্র গঠনের ভিত্তিপত্তন বা উপাদান সংগ্রহ হয় এই সময় হইতেই। এই অবস্থার প্রথম দিক দিয়া শিশুরা হয় গতানুগতিকপন্থী, অনুকরণপ্রিয় এবং সরল বিশ্বাসী। মাতা-পিতা, গুরুজন বা সহগামীদের চাল চলন, আহার-বিহার ইত্যাদি অনুসরণ করিয়া চলে এবং উহাদের যে কোনো বচন অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করে।
হয়তো কোনো শিশুর মা-বাবা জলডুবি হইবার বা পোকা-মাকড় ও সাপে কামড়াইবার ভয়ে শিশুকে বলিল, পুকুরে কুমির বা বাগানে বাঘ আছে। হয়তো শিয়াল-কুকুরে কামড়াইবার ভয়ে কোনো শিশুকে বলা হইল, “শ্মশানে ভূত ও গোরস্থানে শয়তান থাকে, উহারা শিশুদের পাইলে ঘাড় মটকায়, ঐসব জায়গায় কখনও যাইবে না” ইত্যাদি। যদিও এই জাতীয় উপদেশগুলির উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু কুমির, বাঘ, ভূত ও শয়তান সবই মিথ্যা। তথাপি সরলমতি শিশু উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিল এবং উপদেশগুলি পালনের সুফলও লাভ করিল। এই কথা সত্য যে, তখন ঐ উপদেশগুলি বিশ্বাসপূর্বক পালন না করিলে হয়তো শিশুরা মহাবিপদে পতিত হইত।
সভ্যতার বাল্যাবস্থা –এই অবস্থায় সমাজের অধিনায়ক ছিলেন মুনি-ঋষি, নবী-আম্বিয়া বা আঞ্চলিক জ্ঞানী ব্যক্তিরা। জীবনের মানোন্নয়নের জন্য জনসাধারণকে তাঁহারা নানারূপ উপদেশ দিতেন। উপদেশকের আসল উদ্দেশ্য ছিল মানব জীবনের উৎকর্ষ সাধন। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য তাহারা কখনও নানাবিধ কাল্পনিক কাহিনী বা উপাখ্যান রচনা করিয়া সাধারণকে শুনাইতেন, যাহার মধ্যে নিহিত থাকিত চরিত্র গঠন ও জাতীয় উন্নতির প্রেরণা। শুধু নিজেরাই বলিতেন না, বলাইতেন– জীব-জন্তু, দেব-দেবী বা ঈশ্বরকে দিয়াও। তাহারা মন্দ কাজের জন্য ভয় দেখাইতেন এবং ভালো কাজের জন্য অভয় দান করিতেন। তবে ভীতিকরগুলি পুকুরের কুমির ও বাগানের বাঘের মতো বসতবাড়ির কাছাকাছি থাকিত না, থাকিত বহুদূরে, মানুষের দৃষ্টিসীমার বাহিরে (পরকালে)।
মানুষের ব্যক্তিজীবনে এই অবস্থাটি প্রতিফলিত হয় ৫-৬ হইতে ১০-১১ বৎসর বয়সের মধ্যে এবং সমাজপতি বা উপদেশকের ভূমিকা গ্রহণ করেন পাঠশালা, মক্তব ও টোলের পাঠ্যপুস্তক প্রণেতাগণ এবং শিক্ষকবৃন্দ।
সভ্যতার কৈশোরাবস্থা –এই অবস্থায় সমাজপতিরা বনিয়াছেন রাজ্যপতি। মানবতাবিরোধী বা নীতিগর্হিত কাজের জন্য নানাবিধ হিতোপদেশ দান ও নরকবাসের ভয় দেখাইয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না রাজ্যপতিরা সমাজপতিদের মতো, তাহারা ব্যবস্থা করিতেন কারাবাস, বেত্ৰদণ্ড ইত্যাদির। সমাজপতিদের আয়ত্তে ছিল শুধু ভাষণ ও তোষণ, কিন্তু রাষ্ট্রপতিরা করিতেন শাসন ও পোষণ।
সমাজপতি বা মান্ধাতার আমলের অতিপ্রাকৃতিক বা অলৌকিক কাহিনীগুলি এই সময়ে আর সকলে বিশ্বাস করিতে চাহিলেন না। কার্য-কারণ সম্পর্ককে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিল দার্শনিক মতবাদ। ফলে দ্বন্দ্ব বাধিল বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী –এই দুই দলে।
সভ্যতা বিকাশের উপরোক্ত অবস্থাটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব বিস্তার করে ১২-১৩ বৎসর বয়স হইতেই। উহার প্রকট রূপ দেখিতে পাওয়া যায় ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আধুনিক শিক্ষায়তনগুলিতে এবং অনেকটা বাহিরেও।
সভ্যতার যৌবনাবস্থা —এই অবস্থাটি হইল মানব সভ্যতার বর্তমান অবস্থা। ইহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। কেননা, জনসাধারণ ইহার প্রত্যক্ষদর্শী এবং প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে উহার বিবৃতি দেওয়া নিরর্থক।
এই সময়টিকে বলা হয় বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞান হইল মানবীয় জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থা এবং মানব সভ্যতার যৌবনাবস্থাও বটে। এই যুগে যুগমানবের আসনে সমাসীন বিজ্ঞানীরা, সমাজপতিরা নহেন। বিজ্ঞানীরা হইলেন নীরব সাধক। কোনো মতবাদ অটুট রাখিবার বা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বিজ্ঞানীরা কখনও কোনোরূপ হৈ-চৈ করেন না। বিশেষত কোনো মতবাদকে সামান্য আঘাতে ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ভয়ে মুরগির ডিমের মতো পাখার নিচে পুঁজিয়া রাখেন না, উহা ছাড়িয়া দেন বিশ্বের দরবারে –সত্যমিথ্যা যাচাইয়ের জন্য।
এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট হইল –১. গতানুগতিকতা বর্জন করা, অর্থাৎ স্বয়ং কিছুই না বুঝিয়া অন্যের দেখাদেখি কোনো কাজ না করা; ২. কোনোরূপ আপ্তবাক্য গ্রহণ না করা, অর্থাৎ কোনো কথা সত্য কি মিথ্যা তাহা যাচাই না করিয়া শুধু গুরুবাক্য বলিয়া বা বক্তার নামের জোরেই বিশ্বাস না করা ইত্যাদি।
সভ্যতা বিকাশের উপরোক্ত অবস্থাটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে প্রস্ফুটিত হয় যৌবনে। কেননা, এই সময়টিই মানুষের ব্যক্তিগত জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থা। কিন্তু কেহ যদি ৬০ বৎসর বয়সেও তাহার মুরুব্বিদের সেই শৈশবকালের উপদেশ মানিয়া চলেন, অর্থাৎ পুকুরে কুমির, বাগানে বাঘ, শ্মশানে ভূত ও গোরস্থানে শয়তান থাকে –ইহা বিশ্বাস করিয়া ঐসকল জায়গায় না যান, তবে তাহাকে কি বলা যায়? তাহাকে বলা যায়– ৬০ বৎসর বয়সের শিশু!
১৩. সভ্যতা বিকাশের কতিপয় ধাপ
সভ্যতা বিকাশের কতিপয় ধাপ
# অগ্নি আবিস্কার
আজকাল অগ্নি উৎপাদন করা আমাদের কাছে একান্তই খেলো। বিজ্ঞানের বদৌলতে রাসায়নিক ও বৈদ্যুতিক নানা উপায়ে অগ্নি উৎপাদন করা হইয়াছে একান্ত সহজ। একটি দেশলাই পকেটে ফেলিয়া উহা দ্বারা মুহুর্মুহু আমরা অগ্নি উৎপাদন করিয়া থাকি। কিন্তু আদিম মানবদের এইসকল সুযোগ-সুবিধা ছিল না। তখন অগ্নি উৎপাদন করা ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ব্যাপার।
অগ্নি দুই প্রকার –প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম।
প্রাকৃতিক অগ্নি
বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, সূর্য একটি অগ্নিপিণ্ড এবং পৃথিবী উহারই একটি অংশ। আদিতে এই পৃথিবীটিও অগ্নিময় ছিল এবং উহা নির্বাপিত হইতে সময়.লাগিয়াছিল লক্ষ লক্ষ বৎসর। ভূপৃষ্ঠ এখন ঠাণ্ডা হইয়া জীববাসের যোগ্য হইয়াছে এবং নানা রকম জীব বাস করিতেছে। ভূপৃষ্ঠের কোথায়ও সেই আদিম অগ্নির নামগন্ধও নাই। তবে সেই আদিম অগ্নির বীজ এখনও সুপ্ত আছে পৃথিবীর কেন্দ্রপ্রদেশে এবং উহার সাক্ষাত পাই আমরা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময়ে। কিন্তু সেই অগ্নি মানুষের স্বার্থের অপেক্ষা অনর্থই ঘটায় বেশি।
এককালে পৃথিবীর অনেক জায়গাই ছিল ঘন বনে আবৃত। লোকবৃদ্ধির সাথে সাথে ভূপৃষ্ঠ ক্রমশ বনশূন্য হইতেছে। সেকালে কোনো কোনো সময় বনমধ্যে কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণের ফলে হঠাৎ আগুন জ্বলিয়া উঠিত এবং তাহাতে বনকে-বন জ্বলিয়া ছারখার হইয়া যাইত ও বনের পশু পাখিরা জ্বলিয়া-পুড়িয়া মারা যাইত। উহাকে বলা হইত দাবানল। দাবানল এতই উগ্রমূর্তি ধারণ। করিত যে, মানুষ বা কোনো প্রাণীই উহার কাছে ঘেঁষিত না। মহাভারতে উক্ত আছে যে, ঐরূপ একটি দাবানলে ইন্দ্রপ্রস্থের নিকটস্থ খাণ্ডব বন দগ্ধ হইয়াছিল। খাণ্ডব অধুনা মধ্যপ্রদেশের নিমার জিলার প্রধান নগর। প্রবাদ আছে যে, ঐখানেই খাণ্ডবদাহ হইয়াছিল। সে যাহা হউক, দাবাগ্নি মানুষের কোনো উপকারে আসে না।
প্রাকৃতিক অগ্নির আর একটি উৎস হইল উল্কা। উল্কারা পতনের সময় বায়ুর ঘর্ষণে জ্বলিয়া উঠে এবং কোনো কোনো সময় উহারা প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় ভূপতিত হয়। কিন্তু উহা এতই ক্ষণস্থায়ী যে, কোনো মানুষ উল্কার আগুনের নাগাল পায় না।
উল্কাপাতের ন্যায় বজ্রপাতও ভূপৃষ্ঠে অগ্নি বহন করিয়া আনে। কিন্তু উহাও মানুষের কোনো উপকার করে না, করে শুধু অপকার। তবে বর্তমানে কোনো কোনো বিজ্ঞানী কৃত্রিম বজ্রপাতের দ্বারা ভূমি উর্বরা করিবার গবেষণা চালাইতেছেন।
কৃত্রিম অগ্নি
সচরাচর আমরা যে আগুন ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা হইল কৃত্রিম আগুন। এই আগুন কখন কাহারা আবিষ্কার করিয়াছিল, তাহা সঠিক বলিবার উপায় নাই। মানব সভ্যতার একটি প্রধান ধাপ আগুনের আবিষ্কার।
পুরাতত্ত্ববিদগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, মানুষ এককালে পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করিত। একখানা পাথরকে আর একখানা পাথর দিয়া ঠুকিয়া ঠুকিয়া মনের মতো আকার দেওয়া বা দেওয়ার চেষ্টা করা হইত। পাথরে পাথর ঠুকিলে অনেক সময় তাহা হইতে ফুলকি নির্গত হইয়া থাকে এবং উহা ঐ সময়ও হইয়াছিল। বোধ হয় যে, ঐ রকম ফুলকিকে ভিত্তি করিয়া বা কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া পুরানো পাথর যুগেই আগুনের আবিষ্কার হইয়াছিল।
আগুন আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ মানুষ’ নামের অধিকারীই ছিল না। তখনকার মানুষদিগকে বলা যাইতে পারে– দ্বিপদ পশু না হইলেও দ্বিপদ জানোয়ার; কেননা, আগুন আবিষ্কারের পূর্বে বা কিছুকাল পরেও উহারা মাছ-মাংস কাঁচাই ভক্ষণ করিত। আদিম মানুষদের মাছ-মাংস কাঁচা ভক্ষণ করা যে কতটুকু কষ্টসাধ্য ছিল, তাহা ভাবাও সহজ নহে। মাছগুলিকে না হয় আঁচড়াইয়া-কামড়াইয়া থেঁতো করিয়া কোনো রকম উদরস্থ করা যাইত, কিন্তু গণ্ডার, ভালুক ইত্যাদি বড় বড় জন্তুগুলির চামড়া বা মাংস ছেঁড়া বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। বিশেষত হাতের ও সঁতের জোর ভিন্ন হাতিয়ারের জোর পাথর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তথাপি যে রকম করিয়াই হউক, উহারা যে ঐসকল জন্তুর মাংস ভোজন করিত, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। আদিম মানবদের আস্তানার কাছাকাছি ঐ জাতীয় জন্তুদের হাড়গোড় দেখিয়া।
ফুলকির আগুনের দ্বারা খড়-কুটা জ্বালানো সহজ ব্যাপার নহে। কোথায়ও কোনোরূপ কায়ক্লেশে আগুন জ্বালাইতে পারিলে গোটা অঞ্চল উহাকে বীজরূপে ব্যবহার করিত এবং আগুনটিকে অনির্বাণ রাখা হইত। বর্তমান কালেও কোনো কোনো ধর্মমন্দিরে অনির্বাণ অগ্নি রক্ষার নিয়ম আছে।
আগুনের তাপ ও আলোর অলৌকিক শক্তি দেখিয়া আদিম মানবেরা বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিল নিশ্চয়ই। তাহারা দেখিয়াছিল যে, অগ্নির কোমল দেহের কঠিন আঘাত সহ্য করিতে বাঘ, ভালুক বা হাতিও পারে না। আগুন দেখিলে উহারা কেহই উহার কাছে আসিতে সাহস পায়। না। সুতরাং আগুন দ্বারা হিংস্র জন্তু তাড়ানো যায়। আগুনে সেঁক দিলে মাছ-মাংস কোমল ও সুগন্ধী হয় (আগুনে সেঁকা মাংস ‘কাবাব’ খাওয়ার রেওয়াজ এখনও কিছু কিছু আছে)। আগুনকে দেখিলে বাঘ-ভালুকের অপেক্ষাও দ্রুত পালায় অন্ধকার। অন্ধকার ছিল আদিম মানবদের চিরশত্রু ও চিরসহচর। কেননা চাঁদ-সূরুজের উপস্থিতি ভিন্ন জীবনের বাকি সময় অন্ধকারেই কাটাইত আদিম মানবেরা। অন্ধকার প্রহরগুলি উহাদের শুইয়া, বসিয়া, জাগিয়া বা ঘুমাইয়া কাটাইতে হইত; কেহ কাহারও মুখ পর্যন্ত দেখিতে পাইত না। আগুন আবিষ্কারের পর দেখা গেল যে, আগুনের আলোয় রাত্রেও দেখা-সাক্ষাত ও কাজকর্ম করা বেশ চলে। বিশেষত দারুণ শীতের সময় যখন দেহ ঠকঠক করিয়া কাপিতে থাকে, তখন আগুনের কাছে আসিলে দেহ চাগা হয়।
আদিম মানবেরা লক্ষ্য করিয়াছিল, আগুনের একটি আশ্চর্য ক্ষমতা এই যে, আগুনে পোড়াইলে কোনো পদার্থেরই পূর্বরূপ বজায় থাকে না; জীব বা উদ্ভিদ, এমনকি মাটি পাথরেরও। আগুন বহু রূপকে পরিণত করে এক রূপে, অগার বা ভস্মে।
মানুষ তখন আর শিয়াল-কুকুরের মতো কঁচামাংসভোজী নহে, সে তখন সেঁকা বা পোড়ামাংসভোজী জীব। যখন তাহারা লক্ষ্য করিল যে, মাটি পোড়াইলে উহা কাষ্ঠাদির ন্যায় কয়লা বা ভস্মে পরিণত হয় না বটে, কিন্তু কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন এই তথ্যটির সাহায্যে বানানো হইল পোড়ামাটির পাত্র। শুরু হইল মাছ-মাংস রান্না করিয়া খাওয়া। কিন্তু এই রান্নার অর্থ আধুনিক রান্না নহে। উহাতে হলুদ-মরিচ বা তৈল-লবণের সম্পর্ক ছিল না, উহা ছিল মাছ মাংস সিদ্ধ করিয়া খাওয়া।
আগুন আবিষ্কারের পর মানুষ পশুর কোঠা পার হইয়া অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু একদল ভাবুক তাহাদের ভাবনা চালাইলেন অন্য পথে। তাহারা ভাবিলেন, অগ্নি আমাদের পরম উপকারী এবং সময়ে অপকারীও বটে। সুতরাং উপকারের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও অপকারের জন্য উহার স্তুতিগান করা উচিত। অগ্নিকে কল্পনা করা হইল ব্যক্তি রূপে, দেওয়া হইল দেবত্ব, প্রবর্তিত হইল উহার পূজার বিধি।
প্রথমে ভারতের দিকেই চাহিয়া দেখা যাক, ভারতীয়রা আগুনকে লইয়া তাহাদের কল্পনার ঘোড়া দৌড়াইয়াছেন কতদূর। কথিত হয়, পরম পুরুষের মুখ হইতে ইহার জন্ম হয়। মতান্তরে ধর্মের ঔরসে বসুভার্যার গর্ভে অগ্নির জন্ম হয়। ঋগ্বেদে বর্ণিত আছে যে, অগ্নি স্থুলকায়, রক্তবর্ণ ও লম্বোদর; হঁহার কেশ, শ্মশ্রু, ভূ ও চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ; হস্তে শক্তি ও অক্ষসূত্র। ইহার বাহন ছাগ।
অগ্নি একজন দিকপাল, পূর্ব ও পশ্চিম দিকের অধিপতি। হঁহার স্ত্রীর নাম স্বাহা। মহাভারতে উক্ত আছে যে, একদা স্বেতকী রাজার যজ্ঞে প্রচুর পরিমাণে হবিভোজন করিয়া অগ্নির পেটে অসুখ হইয়াছিল। ব্রহ্মার নিকট রোগের প্রতিকারের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি অগ্নিকে বলিলেন যে, খাণ্ডব বন দগ্ধ করিতে পারিলে তোমার রোগ আরোগ্য হইতে পারিবে। অনন্তর অগ্নি খাণ্ডব বন দগ্ধ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।
কিন্তু দেবাশ্রিত বন সহজে দগ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন না বুঝিতে পারিয়া অগ্নি কৃষ্ণার্জুনের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। অর্জুন সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন বটে, কিন্তু বলিলেন যে, দেবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইলে যে সকল অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োজন, তাহা তাহার নাই। অগ্নি অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ করিয়া দিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়া স্বীয় সখা বরুণদেবের নিকট গমনপূর্বক অনেকগুলি অস্ত্র সংগ্রহ করিলেন। তাহা হইতে কপিধ্বজ রথ, গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় অর্জুনকে এবং সুদর্শন চক্র, কৌমোদকী গদা কৃষ্ণকে প্রদত্ত হইল। খাণ্ডব বন দহনে দেবগণ বাধা দিলে কৃষ্ণার্জুনের সহিত তাহাদের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে দেবগণ হারিয়া গেলেন। অগ্নি খাণ্ডব বন দগ্ধ করিলে তাহার পেটের অসুখ সারিয়া গেল।
পারসিকগণ মনে করেন যে, অগ্নি মঙ্গলময়, তাহাদের ইহকাল ও পরকালের মগল বিধান করিবেন অগ্নি। তাই তাহাদের পরমারাধ্য দেবতাই হইলেন অগ্নি।
ইহুদিগণ মনে করেন যে, মাংসপোড়া পূতগন্ধ মানুষের কাছে যখন লোভনীয়, নিশ্চয়ই উহা জাভে (ইহুদিদের ঈশ্বর)-এর নিকটও লোভনীয়। তাই ইহুদিরা জাভে-এর তুষ্টার্থে গো-মেষাদি বলি দিয়া উহার মাংস অগ্নিদগ্ধ করিয়া আকাশে ধুয়া উড়াইতেন।
.
# কৃষি ও পশুপালন
সেমিটিক জাতির মতে, কৃষি ও পশুপালন শুরু করিয়াছিলেন বাবা আদম বেহেশত হইতে পৃথিবীতে আসিয়াই। হালের বলদ, লাঙ্গল-জোয়াল ও ফসলের বীজ বেহেশত হইতে আমদানি হইয়াছিল কি না, তাহা জানি না, তবে তিনি নাকি চাষাবাদ করিয়াই জীবন যাপন করিতেন। তাহার চাষের ফসল ছিল বোধ হয় গন্ধ)ম। কেননা, তিনি নাকি খাইতে ভালোবাসিতেন উহাই।
সেকালের মিশরবাসীদের লাগলে ছিল একটি ফাল ও দুইটি হাতল। একজন চাষী দুই হাতে হাতল চাপিয়া ধরিত এবং অপর একজন গরু তাড়াইত, জোয়াল জোড়া হইত গরুর শিং-এর সাথে।[২৯] বাবা আদমের লাগলের আকৃতি কিরূপ ছিল, জোয়াল কিভাবে জুড়িতেন এবং রশা রশি কোথায় পাইয়াছিলেন –সেই বিষয়ে কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না।
পুরাতত্ত্ববিদগণের মতে, কৃষি ও পশুপালন কোনো বিশেষ ব্যক্তির দ্বারা কোনো এক সময়ে প্রবর্তিত হয় নাই। উহা হইয়াছে বহু দেশের, বহু লোকের, বহু দিনের প্রচেষ্টার ফলে। তবে কৃষি ও পশুপালন বা মানব সভ্যতার কেন্দ্রভূমি হিসাবে ধরা হয় মিশর, মেসোপটেমিয়া ও ভারতবর্ষের সিন্ধু প্রদেশকে।
কৃষি ও পশুপালন –ইহার কোনটি আগে শুরু হইয়াছে, তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। হয়তো সমসাময়িক, নচেৎ পশুপালন কিছুটা আগের। পশুপালন আরম্ভ হইয়াছিল শিকারী যুগেই।
কৃষি ও পশুপালন প্রচলিত হইবার পূর্বে আদিম মানবদের খাদ্যব্যবস্থা ছিল পশু-পাখিদের মতো। সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে দল বাঁধিয়া উহারা খাদ্যের সন্ধানে বাহির হইত এবং সমস্ত দিন ঘোরাফেরা করিয়া পশু-পাখি শিকার বা ফল-মূল সংগ্রহ যাহা করিতে পারি, তাহা দিয়াই উদরপূর্তি করিয়া আস্তানায় আসিয়া নিদ্রা যাইত। আবার প্রভাতে যাত্রা, ঘোরাফেরা, জোটে তো খাওয়া, আর না জোটে তো না খাওয়া, সন্ধ্যায় আস্তানায় আসিয়া শোয়া। এইরূপ চলিত আদিম মানবদের জীবন যাপন। উহাদের কোনোরূপ সঞ্চয় বা মজুদ খাদ্য ছিল না, ছিল যখন পাওয়া তখন খাওয়া। আবার সকল দিন সমান যাইত না। হয়তো কোনদিন প্রচুর খাদ্য জুটিত, আবার কোনোদিন আদৌ জুটিত না।
হিন্দুদের ঈশ্বর নাকি গোমাংস ভক্ষণে নিষেধ করিয়াছেন, আবার মুসলমানদের আল্লাহ বলিয়াছেন, “শূকরের মাংস খাইও না”। কিন্তু খ্রীস্টানদের প্রভু বলিয়াছেন গরু ও শূকর উভয়ই খাইতে। কিন্তু খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে ঈশ্বরপ্রদত্ত কোনো তালিকা ছিল না আদিম মানবদের কাছে। তাহারা খাদ্য নির্বাচন করিত উহা পাইবার ও খাইবার সুযোগ-সুবিধা মতো। আজিও দেখা যায় যে, ধর্মরাজ্যের বাহিরের বিভিন্ন উপজাতি ও অসভ্য সমাজে ছাগল, গরু, বাঘ, ভালুক, শূকর, কুমির, সাপ, ইঁদুর, ব্যাঙ ইত্যাদি খাওয়া হইতেছে সবই।
কোনো কোনো সময় শিকারীদের হাতেই কতক পশু জীবন্ত ধরা পড়িত। তখন আবশ্যকীয় খাদ্যের জোগান থাকিলে ঐগুলিকে আর বধ করা হইত না, বাঁধিয়া রাখা হইত –যেদিন শিকার। জুটিবে না, সেইদিন খাইবার জন্য। আবার কোনো কোনো সময় নিরীহ পশুর বাচ্চাদের বন। হইতে ধরিয়া আনা হইত। খাদ্যের অভাব না হইলে ঐরূপ কোনো কোনো পশু দীর্ঘদিন বাঁধা থাকিত এবং তখন দেখা যাইত যে, উহাদের সকলেই ছুট পাইলে পালায় না, আস্তানার কাছে। কাছে ঘোরাফেরা করে ও শিকারীদের দেওয়া খাবার খায়।
আদিম মানবেরা যখন দেখিল যে, দুই-চারিটি পশু এইরূপ মজুদ রাখিতে পারিলে তাহাদের আর খাদ্যের অনিশ্চয়তা থাকে না, তখন ঐ জাতীয় পশুদের আর সহজে বধ না করিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিল। ইহাতে দেখা গেল যে, সময়ে উহারা বাচ্চা প্রসব করে এবং পালের। পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অধিকন্তু উহাদের দুগ্ধও ব্যবহার করা চলে। অবস্থা যখন এইরূপ হইল, তখন দলের সকলেই শিকারে বাহির না হইয়া কেহ কেহ থাকিতে লাগিল পালিত পশুর তত্ত্বাবধানে রাখালরূপে। এইভাবে হইয়াছিল পশুপালনের সূত্রপাত। অনেকের মতে আদিম। মানবদের প্রথম পালিত পশু ছিল বুনো ভেড়া ও বুনো ষড়।
কুকুর মানুষের পোষ মানিয়াছিল গবাদি পশু পোষ মানিবার অনেক আগেই। আদি মানবদের আস্তানার আশেপাশে পড়িয়া থাকিত বন্য পশুর হাড়গোড় ও ত্যাজ্য অংশ। একদল নেকড়ে জাতীয় বন্য পশু (কুকুর) উহা খাইতে আসিত ও আস্তানার কাছে কাছে নির্ভয়ে ঘোরাফেরা করিত, তাড়াইয়া দিলেও আবার আসিত। শিকারীরা উহাদের কিঞ্চিৎ সহানুভূতি দেখাইলে উহারা শিকারীদের অনুগত ও সহচররূপে গণ্য হইয়াছিল।
কালক্রমে গবাদি পালিত পশুর সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়া অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইল যে, সংবৎসর উহাদের দুগ্ধ ও মাংস খাইলেও উহাদের সংখ্যা বাড়ে বৈ কমে না, তখন বন্যপশু শিকার ত্যাগ করিয়া দলের সকলেই মনোযোগ দিল পশুপালনে। কিন্তু অচিরেই একটি অসুবিধায় পড়িতে হইল পশুপালকদের। স্থায়ী আস্তানায় থাকিয়া শত শত বা হাজার হাজার পশুর খাদ্য জোগানো হইল অসম্ভব। কাজেই উহারা আস্তানা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল অন্য অঞ্চলে পশুপাল সহ। সেখানকার তৃণাদি পশুখাদ্য নিঃশেষ হইলে আবার খোঁজ করিতে ও চলিয়া যাইতে হইত যেখানে তৃণসমাকুল মাঠ আছে সেখানে। এইভাবে পশুপালনরত ভ্রাম্যমান মানবদলসমূহই বনিয়াছে যাযাবর জাতি।
শিকার ও সংগ্রহের যুগের প্রথম দিকে নারী ও পুরুষের কাজের ভাগাভাগি ছিল না। সকলে মিলিয়া দল বাধিয়া বাহির হইত ও ছোট ছোট জন্তু-জানোয়ার তাড়াইয়া-ঝাপাইয়া হাতেই ধরিত এবং এই কাজে মেয়েরা যথাসাধ্য সাহায্য করিত। কিন্তু বল্লম আবিষ্কারের পর যখন হরিণ, মহিষ ও ভালুকাদি বড় বড় জন্তু শিকার শুরু হইল, তখন আর সেই কাজে মেয়েদের সাহায্য করা সম্ভব হইল না। কেননা মেয়েদের উপর আর একটি অতিরিক্ত কাজের ভার ছিল— শিশুপালন। মেয়েরা তখন বনে বনে ঘুরিয়া ফলমূল সংগ্রহ করিত মাত্র।
সেই আদিম কালের মেয়েরা ফলমূল সংগ্রহ করিবার সময় এমন দুই-একটি ফলের থোকা পাইয়াছিল যে, উহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলগুলি বেশ সুস্বাদু ও পুষ্টিকর। ফলগুলি ক্ষুদ্র বলিয়া উহা যখন তখন খাওয়া চলিত না। তাই ঐগুলি আস্তানায় লইয়া আসিত এবং অবসর সময়ে খুঁটিয়া খুঁটিয়া উহার দানা খাইত। হয়তো ঐ রকম দুই-চারিটি ফলের গোটা আস্তানার আশেপাশে পড়িয়া তাহা হইতে গাছ জন্মিত ও ফল ধরিত। মেয়েরা যখন উহার উৎপত্তি সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হইল, তখন বুঝিতে পারিল যে, দানাগুলি সরস মাটিতে চাপা থাকিয়াই উহাদের অকুরোদগম হইয়াছে। তাই উহারা সরস মাটিতে বীজ পুঁতিয়া গাছ জন্মাইয়া উহা হইতে বেশি বেশি ফসল পাইতে লাগিল এবং খুঁটিয়া খাওয়ার পরিবর্তে পাথরে পিষিয়া উহার মণ্ড ভক্ষণ শুরু করিল। ইহাতে। ফলমূল সংগ্রহের ব্যাপারে উহারা অনেকটা আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠিল। এইভাবে আদিম কালের মেয়েদের হাতেই প্রবর্তন হইল গম ও বার্লির চাষ অর্থাৎ কৃষিকাজের সূচনা। বস্তুত পৃথিবীতে কৃষিকাজের প্রবর্তন করিয়াছে নারীরা, যীশু খ্রীস্ট জন্মিবার প্রায় সাড়ে চারি হাজার বৎসর আগে।[৩০]
গরু মহিষের শিং, সূঁচালো কাঠ বা অনুরূপ অন্য কিছুর দ্বারা খেচাইয়া খোঁচাইয়া মাটি আলগা করিয়া বীজ বপন করাই ছিল তখনকার দিনের কৃষি। বোঝাই যাইতেছে যে, এইভাবে বেশি জমি চাষ করা সম্ভব নহে। কৃষিকাজের সামান্য প্রসার হইয়াছিল কোদাল আবিষ্কারের পর। সে কিন্তু আধুনিক কোদাল নহে। হরিণের শিং, বাঁকানো কাঠ বা কাঠে বঁধা একখণ্ড সূঁচালো পাথর মাত্র। উহা দ্বারা কোপাইয়া (খোঁচাইয়া নহে) মাটি আলগা করিয়া বীজ বপন করা হইত। এই ব্যবস্থামতো শত শত বৎসর কৃষিকাজ চালাইয়াছিল আদিম মানবেরা। এই সময়টিকে বলা হয় কোদাল দ্বারা চাষ করার যুগ, সংক্ষেপে কোদাল যুগ। এই যুগে চাষ বা ফসলের মাত্রা কিছু বাড়িয়াছিল বটে, কিন্তু শিকার ও সংগ্রহ ত্যাগ করিয়া মানুষ স্বাবলম্বী হইতে পারে নাই। তবে। শিকারের তাগিদ কিছু কমিয়াছিল।
যীশু খ্রস্টের জন্মের তিন হাজার বৎসর আগেই মিশর, মেসোপটেমিয়া এবং ইহার কিছুকাল। পরে ভারতবর্ষ, সাইপ্রাস, চীন ও গ্রীসে বঁড় বা গাধা দিয়া লাঙ্গল টানাইবার পরিচয় পাওয়া যায়। তখন শিকার ও সংগ্রহের যুগ শেষ হইয়া আসিয়াছে। কোদাল যুগের পরিবর্তে রীতিমতো কৃষিযুগ শুরু হইয়াছে। আবাদী জমি ও ফসলের পরিমাণ যথেষ্ট বাড়িয়াছে। মানুষ খাদ্যের ব্যাপারে হইতে পারিয়াছে স্বাবলম্বী। বস্তুত খাদ্যসংস্থানে পশু-পাখির পর্যায় হইতে মানুষকে মানুষ পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছে পশুপালন ও কৃষি।
আজকাল যেমন নিতান্ত নীরস ও অনুর্বর মাটিতেও নানান কৌশলে সেচ ও সারের ব্যবহার করিয়া ফসলোৎপাদন করা হইয়া থাকে, আদিতে কিন্তু তাহা ছিল না। তখন চাষের কাজের সম্পূর্ণ নির্ভর ছিল প্রকৃতির উপর। যে দেশের মাটি স্বভাবতই সরস ও উর্বর, মাত্র সেই দেশেই। ব্যাপকভাবে কৃষিকাজ শুরু হইয়াছিল সবচেয়ে আগে। তাই নীল, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস এবং সিন্ধু। নদীর বদৌলতে মিশর, মেসোপটেমিয়া ও ভারতের সিন্ধু প্রদেশে সর্বাগ্রে ব্যাপকভাবে কৃষিকাজ শুরু হইয়াছিল। আর যে দেশের মানুষ বৎসরের এক বিশেষ সময়ে ফসল জন্মাইয়া সংবৎসরের খাদ্যের সংস্থান করিতে পারে, তাহারাই পারে অবসর সময়ে অন্যান্য চিন্তা ও কাজ করিতে। তাই শিল্পক্ষেত্রেও ঐ তিনটি দেশ হইয়াছিল অগ্রণী। কাজেই উক্ত দেশত্রয়কেই বলা হয় মানব সভ্যতার কেন্দ্রভূমি। নানা রকম প্রমাণ হইতে পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন যে, ঐ তিনটি দেশে সভ্যতার জন্ম হইয়াছিল খ্রী. পূ. ৩৫০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে।[৩১]
.
# ধাতু ও গৃহ
বলা হয় যে, পাখিরা বিমানবিহারী জীব। কিন্তু বিমানে বিহার কতক্ষণ? বেশির ভাগ সময়ই উহাদের দাঁড়াইতে হয় বৃক্ষশাখায়। আবার বৃক্ষশাখায় দাঁড়াইয়া থাকা চলে না, বসতে হয়, অন্তত ডিম পাড়া বা ডিমে তা দিবার সময়ে। তাই উহারা খড়কুটা বা অন্য কিছুর দ্বারা একটু স্থান করিয়া লয় বসার, বলা হয় –বাসা। মানুষ যখন বৃক্ষচারী ছিল, যে রকমই হউক, তখন তাহারাও তৈয়ার করিত বাসা। কালক্রমে মাটিতে নামিয়া আসিবার পর মানুষ গিরিগুহা বা বৃক্ষকোটরে বাস করিত। আবার কোনো সময়ে বাসা তৈয়ার করিয়া উহাতে বাস করিত। আজিও আমরা অফিসাদি কর্মস্থল হইতে ফিরিবার সময়ে বলি, “বাসায় যাই”।
আদি মানবেরা গুহাবাসী ছিল বটে, কিন্তু সবসময়েই গুহা পাওয়া যাইত না। তখন পর্বত বা বৃক্ষের গা ঘেঁষিয়া ডালপালা জড়ো করিয়া তাহার উপর লতা-পাতার ছাউনি দিয়া বাসা বানানো হইত, যেন কৃত্রিম গুহা। উহাকে গৃহ বলা চলে না। কেননা উহাতে থাম-খুঁটি বা ভিটি-বেড়া ছিল না। তখন ডালপালা ও লতা-পাতা ইত্যাদি সরঞ্জাম সবই সংগ্রহ করিতে হইত ভাঙ্গিয়া বা ছিঁড়িয়া। যেহেতু হাতিয়ার বলিতে উহাদের কিছুই ছিল না, একমাত্র পাথর ভিন্ন। মানুষ প্রকৃত গৃহবাসী হইয়াছে ধাতু বিশেষত লৌহ আবিষ্কারের পর।
প্রায় পাঁচ লক্ষ বৎসর আগে মানুষ গাছ হইতে নামিয়া মাটিতে চলাফেরা শুরু করে। তখন তাহারা খাদ্য তৈয়ার করিতে জানে না, নির্ভর মাত্র শিকার ও সংগ্রহের উপর। মানুষের এই অবস্থাকে মর্গান বলিয়াছেন বন্যদশা, প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেন পুরানো পাথর যুগ এবং ভূতত্ত্ববিদগণ বলেন প্লিসটোসেন। উক্ত পাঁচ লক্ষ বৎসরের প্রায় পৌনে ষোল আনা সময়ই কাটিয়াছে মানুষের বন্যদশায়।
মানুষ কৃষি ও পশুপালন শিখিয়াছে এবং নিজেরাই খাদ্য উৎপাদন করিতে জানে –মর্গান এই অবস্থার নাম দিয়াছেন বর্বরদশা, প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেন নতুন পাথর যুগ এবং ভূতত্ত্ববিদগণ বলেন হলোসেন। এই যুগটি প্রায় দুই হাজার বৎসর স্থায়ী ছিল।
প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর আগে নীল, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস এবং সিন্ধু উপত্যকায় যে সভ্যতা গড়িয়া উঠে, মর্গান উহার নাম দিয়াছেন সভ্যদশা। এই সভ্যদশার দুইটি ভাগ আছে। যথা –১. তাম্র ও ব্রোঞ্জ যুগ, প্রায় দুই হাজার বৎসর এবং ২. লৌহ যুগ, প্রায় তিন হাজার বৎসর।
ধাতু যুগের শুরুতে পাথরের হাতিয়ারের পরিবর্তে মানুষ তাম্র বা ব্রোঞ্জ দ্বারা হাতিয়ার নির্মাণে সক্ষম হইয়াছিল এবং উহাতে সুবিধাও হইয়াছিল অনেক। কিন্তু লৌহ আবিষ্কারের মতো উহা সুদূরপ্রসারী ছিল না। ব্রোঞ্জ বা তাম্ৰধাতু আজিও আছে এবং শিল্পক্ষেত্রে উহার কিছু গুরুত্বও আছে। কিন্তু আধুনিক সভ্যতা পুরাপুরি নির্ভর করিতেছে লৌহের উপর, ব্রোঞ্জ বা তাম্রের উপর নহে।
লৌহযুগের প্রাথমিক মামুলি হাতিয়ার ছিল কাটারি, কাস্তে, কোদাল, কুড়াল, করাত ইত্যাদি এবং ইহারই সাহায্যে সম্ভব ও সহজ হইয়াছিল ভূমিকৰ্ষণ, বৃক্ষছেদন, গৃহনির্মাণ, নৌকা তৈয়ার ইত্যাদি। ফলে উন্নত হইয়াছিল কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য, এক কথায় জীবনযাপন প্রণালী। প্রকৃতপক্ষে লৌহ আবিষ্কারই করিয়াছে জগতে আধুনিক সভ্যতার ভিত্তিপত্তন।
.
# তাঁত
পবিত্র বাইবেল গ্রন্থের মতে, আদিমানব আদম সৃষ্ট হইয়াছিল খ্রী. পূ. ৪০০৪ সালে। অর্থাৎ এখন (১৯৭০) হইতে প্রায় ছয় হাজার বৎসর পূর্বে। ঐ সময়ে হযরত আদম এদন উদ্যানে (বেহেশতে?) বাস করিতেন এবং তিনি ঐখানে উলঙ্গ ছিলেন। তৌরিতে লিখিত আছে, “তখন সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি কোথায়? তিনি কহিলেন, আমি উদ্যানে তোমার রব শুনিয়া ভীত হইলাম, কারণ আমি উলঙ্গ, তাই আপনাকে লুকাইয়াছি। … আর সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম ও তাহার স্ত্রীর নিমিত্ত চর্মের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাদিগকে পরাইলেন।” (আদিপুস্তক ৩; ৯, ১০, ২১)
জীবতত্ত্ববিদগণ বলেন যে, চেহারায় পশুর কোঠা পার হইবার পরেও আহার-বিহার ও চাল চলনে মানুষ পশুবৎ ছিল এবং উলঙ্গ থাকিত। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে বৃক্ষপত্র বা বল্কল এবং পশুচর্ম পরিধান করিতে থাকে। এমনকি শীত নিবারণের জন্যও তাহারা পশুচর্মই ব্যবহার করিত। বর্তমান যুগেও এস্কিমো বা অনুরূপ অসভ্য জাতিরা পশুচর্ম পরিধান করিয়া থাকে।
পোষাক-পরিচ্ছদে মানুষ সুসভ্য হইতে পারিয়াছে সুতা তৈয়ার ও তাত আবিষ্কারের পরে। বস্তুত সভ্যতা বিকাশের একটি বিশিষ্ট ধাপ হইল বস্ত্রবয়ন বা তঁত আবিষ্কার।
.
# মাল বহিবার কাজে পশু
আদিম মানবেরা মালবহন কাজে ব্যবহার করিত তাহাদের হাত, মাথা, ঘাড়, পিঠ ইত্যাদি। কিন্তু এইভাবে মাল বহন করা, পরিমাণে অল্প ও সামান্য দূরেই সম্ভব। বেশি পরিমাণ মাল লইয়া দেশান্তরে গমন করা ছিল দুঃসাধ্য। কৃষি ও পশুপালনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল যে, কতক পশুর দ্বারা মাল বহনের কাজও করানো যায়, যেমন –ঘোড়া, গাধা, উট ইত্যাদি। দশটি মানুষের বহনযোগ্য মাল হয়তো একটি পশুই অনায়াসে বহুদুর বহন করিয়া লইয়া যাইতে পারে। তাই শুরু হইল মাল বহনের কাজে পশুর ব্যবহার। ইহাতে এক দেশের মানুষের সহিত আর এক দেশের মানুষের লেনদেন অর্থাৎ স্থলপথে বাণিজ্য সম্ভব হইয়াছিল। মানুষকে সভ্যতার আর এক ধাপ উপরে উঠাইয়া দিয়াছিল মাল বহিবার কাজে পশুর ব্যবহার।
.
# চাকা
কোনো ভারি পদার্থ উত্তোলন করিয়া লওয়া অপেক্ষা টানিয়া লওয়া সহজ এবং পদার্থটি গোল হইলে উহাকে গড়াইয়া লওয়া আরও সহজ। গোল পদার্থ গড়াইবার সহজ পদ্ধতিটি লক্ষ্য করিয়াই সেকালের মানুষ করিয়াছিল চাকা আবিষ্কার এবং তাহা হইতে হইয়াছিল টানাগাড়ি, ঠেলাগাড়ি ইত্যাদি মানুষ চালিত গাড়ির সৃষ্টি। চাকা আবিষ্কারের বহু আগেই মানুষ লাঙ্গল টানিবার কাজে পশু ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিল। কাজেই মানুষচালিত গাড়িকে পশুচালিত গাড়িতে রূপায়িত করিতে বেশিদিন লাগে নাই। সেকালের গাড়ির উন্নত সংস্করণ ছিল রথ। উহা দুই বা চারি চাকা বিশিষ্ট অশ্বচালিত গাড়ি। সেকালের রাজ্যপালেরা উহা ব্যবহার করিতেন আনন্দবিহার এবং যুদ্ধের কাজে।
খ্রী. পূ. ১২৮৫ সালে ফেরাউন দ্বিতীয় রেমেসিস হজরত মূসার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। রথে চড়িয়া (যাত্রাপুস্তক ১৪; ২৩, ২৫)। ইহাতে জানা যায় যে, তিন হাজার বৎসরের অনেক আগেও চাকাওয়ালা গাড়ির প্রচলন ছিল। গাড়ি আবিষ্কারের ফলে লোক চলাচল ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছিল।
আদিম মানবেরা যখন হইতে কঁচা মাছ-মাংস ভোজন ত্যাগ করিয়া রান্নাবান্না আরম্ভ করিয়াছে, তখন হইতেই শুরু হইয়াছে মৃৎপাত্র তৈয়ার ও উহার উন্নতির প্রচেষ্টা। কিন্তু চেষ্টা যতই হইয়া থাকুক, উহা সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে নাই চাকা আবিষ্কারের পূর্বে।
শুধু হাতে পিটিয়া-টিপিয়া মাটির পাত্র তৈয়ার করিতে গেলে উহা বাকাচোরা ও এবড়োখেবড়ো হওয়াই স্বাভাবিক। তখনকার যে সকল শিল্পীরা চাকা নির্মাণ ও উহার গবেষণার কাজে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, কোনো চাকার কেন্দ্রবিন্দুতে একটি শলাকা প্রবেশ করাইয়া উহাকে ঘুরাইয়া ছাড়িয়া দিলে, সে অনেক সময় ধরিয়া ঘুরিতে থাকে; তখন উহার ঐ ঘূর্ণায়মান গতি ও শক্তিকে লক্ষ্য করিয়াই শিল্পীরা করিয়াছিলেন কুমারের চাকা আবিষ্কার। আর ইহার ফলে হইয়াছিল মৃৎশিল্পের অভাবনীয় উন্নতি। সভ্যতা বিকাশের একটি বিশেষ ধাপ হইল চাকার আবিষ্কার। অধুনা বাস, ট্রাক, ট্রেন ইত্যাদি শত শত রকম স্থলযান বা গাড়ি উদ্ভাবন করা হইয়াছে এবং উহাতে কল-কৰ্জাও সন্নিবেশিত হইয়াছে নূতন নূতন, কিন্তু ইহার চাকাটি হইল প্রায় তিন হাজার বৎসরের পুরাতন।
.
# নৌকা ও পাল
পদব্রজে যাতায়াতের যতই সুবিধা থাকুক না কেন, আদিম মানবদের জলপথে গমনের কোনো উপায়ই জানা ছিল না, সাঁতার কাটা ভিন্ন। অভিজ্ঞতাবৃদ্ধির সাথে সাথে যখন দেখা গেল যে, কতিপয় ভাসমান কাঠ একত্র বাঁধিয়া লইলে, উহার উপর আরোহণ করিয়া জলাশয় পার হওয়া যায়, তখন হইতে শুরু হইল ভেলার সাহায্যে জলাশয় পার হওয়া। ইহার পরবর্তী কালের মানুষ বড় বড় গাছের আস্ত খুঁড়ি গুঁড়িয়া এক প্রকার নৌকা প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছিল। এই প্রকার নৌকা প্রস্তুতের প্রথা কোনো কোনো অঞ্চলে এখনও আছে। উহাকে বলা হয় গাছ নৌকা। এই নৌকার একটি বিশেষত্ব এই যে, আকারে উহা যত ছোট বা বড় হউক না কেন, উহার গড়ন হয় প্রায় একই রকম। কাজেই আদিম মানবেরা যতদিন গাছ নৌকা ব্যবহার করিয়াছিল, ততদিন পর্যন্ত নৌশিল্পের কোনো উন্নতিই হয় নাই। নৌশিল্পের উন্নতি শুরু হইয়াছে কাঠের তক্তা তৈর করিয়া তদ্বারা জোড়াতালি দিয়া নৌকা প্রস্তুতের কৌশল জানার পর।
তক্তা দ্বারা নৌকা প্রস্তুতের মস্ত বড় সুবিধা হইল এই যে, উহা দ্বারা আবশ্যকমতো যত বড় ইচ্ছা তত বড় এবং যে কোনোও গড়নের নৌকা তৈয়ার করা যায়। কালক্রমে নানা ধরণের নৌকা যথা –বজরা, ময়ূরপঙ্খী বা পানসি, ছিপ, আল্কি ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছিল এবং বড় বড় জলাশয়ে পাড়ি জমানো সম্ভব হইয়াছিল, এমনকি সাগরবুকেও।
জলপথে যাতায়াত সম্ভব এবং ছোট ছোট নৌকা চালানো সহজসাধ্য হইল বটে, কিন্তু বড় বড় নৌকা চালনা করা ছিল অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। কালক্রমে এই কষ্টসাধ্য নৌ-চলাচল সহজসাধ্য হইল, যখন হইতে হইল নৌকায় পাল খাটাইবার ব্যবস্থা। খ্রী. পূ. ৩০০০ বৎসর পূর্বেই পালের নৌকার আবিষ্কার হইয়াছিল।[৩২]
নৌকা ও পাল আবিষ্কারের ফলে দেশান্তরে যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ সুগম হইয়াছিল। মানুষ পাইয়াছিল জলে ও স্থলে অবাধে চলিবার স্বাধীনতা। আধুনিক যন্ত্রযুগের দ্বার পর্যন্ত মানব সভ্যতাকে আগাইয়া দিয়াছে নৌকা ও পাল। বলা বাহুল্য যে, এই যান্ত্রিক জলযানের যুগেও অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পালের নৌকা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।
.
# লিপি ও কাগজ
আদিম মানবদের একের মনোভাব অপরকে জানাইতে মৌখিক আলাপ ও অঙ্গভঙ্গি ভিন্ন অন্য কোনো উপায় ছিল না। জ্ঞানোন্মেষের সাথে সাথে আবিষ্কৃত হইল চিত্রের মাধ্যমে মনোভাব ব্যক্ত করিবার কৌশল। কিন্তু উহা ছিল ভাবপ্রকাশের অতি সংক্ষিপ্ত আভাস মাত্র। যদি বলিতে হইত যে, তিনজন লোক নৌকাযোগে তিনদিনে একটি হ্রদ পার হইয়াছে, তবে চিত্রে দেখাইতে হইত– একখানা নৌকায় তিনজন আরোহী এবং তিনটি সূর্য।
মিশরে চিত্রলিপি শুরু হইয়াছিল প্রায় ছয় হাজার বৎসর পূর্বে। চিত্রলেখা বেশি সময়সাপেক্ষ এবং উহাতে যোগ্যতাও লাগে যথেষ্ট। তাই পরবর্তীকালে ছবি আঁকার বদলে আরম্ভ হইয়াছিল বিভিন্ন ধরণের দাগ কাটিয়া মনোভাব ব্যক্ত করিবার রীতি এবং বিভিন্ন দাগের সমন্বয়ে অক্ষর ও শব্দের সৃষ্টি। বলা বাহুল্য যে, বিভিন্ন দেশের লোক একই রীতির অনুসরণ করে নাই এবং তৎকালীন সকল রকম লিখনপ্রণালীও অধুনা প্রচলিত নাই। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে পুরাকালের যে সমস্ত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এখনও তাহার অনেকগুলির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নাই।
সেকালের চিত্রলিপির পাত্র ছিল সাধারণত গুহাপ্রাচীর, পর্বতগাত্র ইত্যাদি এবং অক্ষরলিপির পাত্র ছিল মৃৎচাকতি, শিলাখণ্ড, পশুচর্ম, ধাতুপাত, বৃক্ষপত্র ইত্যাদি। এইদেশে তাল, কদলী, ভূর্জ ইত্যাদি বৃক্ষপত্রে লিখন প্রচলিত ছিল কিছুদিন আগেও এবং চিঠি বা পুস্তকাদি লিখা হইত উহাতেই। তাই এখনও আমরা চিঠিকে পত্র এবং বইয়ের পৃষ্ঠাকে পাতা বলিয়া থাকি।
খননকার্যের ফলে পাঁচ-ছয় হাজার বৎসর পূর্বের কঁচা বা পোড়ামাটির চাকতির বহু লিপি আবিস্কৃত হইয়াছে। বারোখানা চাকতির উপর লিখিত তিনশত পঙক্তি সমন্বিত গিলগামেশ নামক একখানা মহাকাব্য উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহার কতক পাওয়া গিয়াছে নিনেভ-এ আসুরবানিপাল এর গ্রন্থালয়ের ভগ্নস্তূপের মধ্যে। খ্রী. পূ. তিন হাজার বৎসর আগে প্যালেস্টাইনে লিখন প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণ আছে। ঐখানে শতাধিক শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।
আরবের মজা সমুদ্রের উত্তর-পূর্ব দিকে কোনো পাহাড়ের গুহায় ১৯৪৭ সালে পাওয়া গিয়াছিল কতগুলি মাটির জালার সারি, উহা সরা দিয়া ঢাকা। সরা উঠাইয়া দেখা গেল যে, জালাগুলিতে মেষচর্মের তাড়া ভর্তি এবং তাহার উপর আলকাতরার মতো কালো কালিতে হিব্রু অক্ষরে লেখা প্রাচীন বিধান বাইবেলের কতিপয় অংশ। উহাতে রহিয়াছে খ্রী. পূ. ২২৫ অব্দে লিখিত ‘স্যামুয়েল’! গ্রন্থের নানান অংশ এবং খ্রী. পূ. ১০০ অব্দে লিখিত সম্পূর্ণ ‘ইসায়া’ গ্রন্থ। ঐগুলিকে বলা হয় ডেড সি স্ক্রোল। স্ক্রোলগুলির মধ্যে যীশুখ্রীস্টের নিজের ভাষা আরামাইক-এ লিখিত গ্রন্থও আছে।
আদিম মানবেরা মাটি, পাথর, গাছের পাতা, পশুর চামড়া ইত্যাদিতেই লিখিত। কিন্তু মিশরীয়রা কালি, কলম ও কাগজ আবিষ্কার করিয়াছিল। উদ্ভিদের আঠার সঙ্গে হাঁড়ির গায়ের কালো স্কুল গুলিয়া, সেই গাঢ় তরল পদার্থকে আগুনে জ্বাল দিয়া কালি প্রস্তুত করা হইত এবং খাগের কলম ব্যবহৃত হইত। প্যাপিরাস নামক নলখাগড়া জাতীয় কোনো জলজ উদ্ভিদকে থেঁতো করিয়া মণ্ড তৈয়ার করা হইত এবং উহাকে বিস্তার করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া মসৃণ, শক্ত, হলুদ রঙের কাগজ প্রস্তুত করা হইত। এইরূপে প্রস্তুত হইয়াছিল প্রথম কাগজ। মিশরীয় জলজ উদ্ভিদ প্যাপিরাস হইতেই কাগজের ইংরাজি নাম হইয়াছে ‘পেপার’। কেহ কেহ বলেন যে, সর্বাগ্রে কাগজ প্রস্তুত হইয়াছিল চীন দেশে।
.
# ধর্ম
আদিতে মানুষের মন ছিল পশু-পাখিদের মনের মতোই সরল ও স্বাধীন। তখন মানুষ তাহার যে। কোনো ইচ্ছা বা প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করিতে পারিত ও করিত। জ্ঞানোন্মেষের সাথে সাথে মানুষ। প্রথমে দলবদ্ধ ও পরে সমাজবদ্ধ হইয়া বসবাস করিতে শুরু করিলে, এই দল ও সমাজকে রক্ষা করিতে আবশ্যক হইল ত্যাগ ও সংযমের। আদিতে এই ত্যাগ ও সংযম ছিল স্বেচ্ছাধীন। ক্রমে যখন সভ্যতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন তাহার দল বা সমাজের বন্ধন দৃঢ় করার জন্য সংযমকে বাধা হইল নীতি ও নিয়মের শৃঙ্খলে। ইহাতে মানুষের সেই স্বাধীন প্রবৃত্তিগুলিকে সু ও কু– এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সু প্রবৃত্তিগুলিকে স্বাধীনই রাখা হইল এবং কু প্রবৃত্তিগুলিকে করা হইল বন্দী। এই সু ও কু অর্থাৎ সৎ ও অসৎ কার্যবিভাগ করিয়াছিলেন বোধহয় সেকালের অঞ্চলবিশেষের গোষ্ঠীপতি বা সমাজপতিরা। আর ইহাই ছিল সম্ভবত মানুষের সমাজজীবন উন্নয়নের প্রাথমিক ধাপ।
কালক্রমে মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির সাথে সাথে তৎকালীন বিশিষ্ট জ্ঞানীগণ যখন বিশ্ব-প্রকৃতি সম্বন্ধে ভাবিতে শুরু করিয়াছিলেন এবং চিন্তা করিতেছিলেন মানবজীবনের অতীত ও ভবিষ্যত সম্বন্ধে, তখন হইতে তাঁহাদের মনে জাগিতেছিল দৈবশক্তি বা ঈশ্বর ও পরকাল সম্বন্ধে নানা কথা। এই ঈশ্বর ও পরকাল সম্বন্ধে যাহাদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছিল এবং জনগণের মধ্যে উহার বিশদ ব্যাখ্যা প্রচার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহারাই ছিলেন সেকালের ধর্মগুরু, যেমন –বৈদিক ঋষিগণ, জোরওয়াস্টার, বুদ্ধ প্রভৃতি। ধর্মগুরুরা সংখ্যায় ছিলেন অনেক এবং দেশ ও কালভেদে উঁহাদের সকলের মতামতও এক ছিল না। তবে বুদ্ধাদি দুই-একজন ধর্মগুরু ভিন্ন জগতের প্রায় সকল ধর্মগুরুই দেবতা বা ঈশ্বর ও পরকালে বিশ্বাসী, পার্থক্য মাত্র ঈশ্বরের সংখ্যায়। কেহ বলিয়াছেন, ঈশ্বর এক এবং কেহ বলিয়াছেন, অনেক।
ধর্মগুরুরা নীতিবাক্য প্রচার করিয়াছেন অজস্র। আর উহাতে কাজও হইয়াছে ১৯৮৮ যথেষ্ট। অসংখ্য নর-নারী অসৎকাজ ত্যাগ করিয়া সৎকাজে ব্রতী হইয়াছেন ধর্মগুরুদের কথিত স্বর্গসুখের প্রত্যাশা ও নরকজ্বালার ভয়ে। মূলত পশুবৃত্তি বা স্বেচ্ছাচারিতা ত্যাগ করাইয়া মানুষকে সুসভ্য করিয়া গড়িয়া তুলিবার ব্যাপারে
ধর্মগুরু বনাম ধর্মের দান অপরিসীম। ধর্ম মানুষকে করিয়াছে নীতিপরায়ণ। শিক্ষানীতি, স্বাস্থ্যনীতি, খাদ্যনীতি, অর্থনীতি, যুদ্ধনীতি, শাসননীতি ইত্যাদি এমন কোনো নীতি নাই, যাহা ধর্মগুরুরা প্রচার করেন নাই। জন্মনীতি, মৃত্যুনীতি, যৌননীতি, বাহ্য-প্রস্রাব, এমনকি জলশৌচ করারও নীতি প্রচারিত হইয়াছে; তবে এককালে ঐ সবের আবশ্যকও ছিল।
ধর্মীয় নীতি বা নিষেধাজ্ঞাসমূহের অনেকগুলি যুগোপযোগী হইলেও উহার যাবতীয় বিধি নিষেধকে প্রচার করা হইয়াছে চিরস্থায়ী বলিয়া। কিন্তু যুগ বদলের সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যক হইয়াছিল উহার কিছু কিছু সংশোধনের এবং সংশোধন শুরু হইয়াছিল মধ্যযুগেই।
ধর্মগুরুরা শাসক ছিলেন না, ছিলেন উপদেশক। কেননা আদিতে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল না, ছিল পুরোহিততন্ত্র। মধ্যযুগে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে, যখন দেখা গেল যে, শুধু নীতিবাক্য আওড়াইয়া এবং পাপ আর নরকের ভয় দেখাইয়া মানুষকে সৎপথে রাখা যায় না, তখন ধর্মগুরুদের পিছনে রাখিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলেন রাষ্ট্রপতিরা; পাপকে অপরাধ আখ্যা দিয়া পরকালের শাস্তির পূর্বেই তাহারা শুরু করিলেন অর্থদণ্ড, কারাদণ্ড, হস্তচ্ছেদন, চাবুকাঘাত ইত্যাদি আশু শাস্তির ব্যবস্থা। আবার বর্তমান যুগে ধর্মীয় নীতির তালিকাভুক্ত প্রায় সমস্ত নীতিই হইয়াছে রাষ্ট্রনীতির তালিকাভুক্ত এবং স্বর্গ বা নরকবাসের পূর্বে হইয়াছে দণ্ড ও পুরস্কারের বিধান।
অধুনা আন্তর্জাতিক নীতিতে কতক ধর্মীয় নীতি পড়িয়াছে বাতিলের পর্যায়ে। যেমন –অবরোধ প্রথা, চিত্রাঙ্কন, গান-বাজনা, খেলাধুলা, কুসীদ গ্রহণ, মদনমিরাস ইত্যাদি বিষয়ক নীতিসমূহ।
ধর্মীয় শিক্ষার ফলে আদিম মানবদের লাভ হইয়াছে যথেষ্ট। এবং বর্তমান যুগেও উহার আবশ্যকতা ফুরায় নাই।
.
আধুনিক সভ্যতা
বর্তমান যুগটিকে বলা হয় বিজ্ঞানের যুগ এবং যন্ত্রযুগও। বিজ্ঞানের যুগ বলা হয় এই জন্য যে, পূর্বে যে কোনো তত্ত্ব নির্ণয় করিতেন সেকালের তত্ত্বজ্ঞানীরা নিজেদের অনুমান ও কল্পনার সাহায্যে এবং উহা জনসমাজে গৃহীত হইত বিশ্বাসের ভিত্তিতে। কেননা তখন পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ রীতি ছিল না। আর বর্তমান যুগে কোনো তত্ত্বই তত্ত্ব বলিয়া গৃহীত হয় না, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ ছাড়া। এই পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণই হইল বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি। আজ ভূতত্ত্ব, আকাশতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব, শরীরতত্ত্ব, প্রাণতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি সমস্ত তত্ত্বই নির্ণীত হইয়া থাকে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ রীতিতে, অর্থাৎ জ্ঞানের ভিত্তিতে। গান, বাজনা, চিত্র ইত্যাদি শিল্পকলা এমনকি সমাজ বা রাষ্ট্রবিধানও আজ বিজ্ঞানভিত্তিক। তাই এই যুগটিকেই বলা হয় বিজ্ঞানের যুগ।
এই যুগের মানুষ কোনো কাজই শুধু গায়ের জোরে করিতে চাহে না, চাহে কৌশলে অর্থাৎ যন্ত্রের সাহায্যে করিতে। নানাবিধ কাজ অতি সহজে সম্পন্ন করিবার জন্য অধুনা এত অধিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, সেই সবের নাম জানা বা সংখ্যা নির্ণয় করাই মুশকিল। এই জন্য এই যুগটিকে বলা হয় যন্ত্রযুগ।
আজকাল যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে হাজার হাজার রকম এবং প্রতিটি আবিষ্কারই মানব সভ্যতাকে কিছু না কিছু আগাইয়া দিয়াছে সম্মুখের দিকে। কিন্তু সকল রকম আবিষ্কার বা যন্ত্রের মূলে রহিয়াছে তিনটি প্রধান আবিষ্কার। যথা –বাষ্পীয়, বৈদ্যুতিক ও পারমাণবিক শক্তি।
.
# বাষ্পীয় শক্তি
প্রকৃতপক্ষে আধুনিক সভ্যতার প্রধান উৎস বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কার। এই শক্তিটি আবিষ্কারের পূর্বে যে সকল মামুলি ধরণের যন্ত্র বানানো হইত, তাহা চালানো হইত মানুষ বা পশুর শক্তিতে এবং তাহাতে কাজ পাওয়া যাইত সামান্য। তখনও কোনো কোনো দেশে রেল বসানো রাস্তা ছিল, কিন্তু উহাতে মালগাড়ি চলিত গাধার সাহায্যে এবং ঘোড়ার সাহায্যে চলিত ডাকগাড়ি।
একটি প্রবাদ আছে যে, জেমস্ ওয়াট একদা একটি কেতলির ফুটন্ত পানি হইতে বাষ্প নির্গত হওয়ার দৃশ্য দেখিয়া বাষ্পীয় শক্তির সন্ধান পান। সুতরাং বাষ্পীয় শক্তির আবিষ্কারক তিনিই। বস্তুত মানুষ বাষ্পীয় শক্তির সন্ধান পাইয়াছিল ইহার অনেক আগেই এবং বাষ্পীয় ইঞ্জিনও তৈয়ার হইয়াছিল ওয়াটের আগে। তবে উহা তেমন কার্যকর ছিল না এবং উহার ব্যবহার হইত শুধু কয়লার খনিতে।
জেমস ওয়াটের স্টিম ইঞ্জিন তৈয়ারের প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে ডার্টমাউথ নিবাসী নিউকোমেন একটি স্টিম ইঞ্জিন নির্মাণ করিয়াছিলেন। এইটিও ব্যবহৃত হইত কয়লা উত্তোলনের কাজে। তবু বিংশ শতকের প্রথম দিকেই বাষ্পচালিত এইরূপ টারবাইন নির্মাণ করা হইয়াছিল, যাহার এক একটির সাহায্যে ৪৩,৭০০টি অশ্বের শক্তির সমান কাজ করা সম্ভব ছিল।
যদিও ওয়াট বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের আবিষ্কর্তা নহেন, তবুও তাহাকে বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের ‘জনক’ বলা হয়। বস্তুত ফুটন্ত পানি হইতে উৎপন্ন বাষ্পকে জগদ্ব্যাপী মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করার উন্নততর পদ্ধতি প্রথমে তিনিই দেখাইয়াছেন। জলযানে স্থাপিত হইল বাষ্পীয় ইঞ্জিন এবং জর্জ স্টিফেনসন নির্মাণ করিলেন বাষ্পীয় রেল ইঞ্জিন। বিভিন্ন বিজ্ঞানীর গবেষণার ফলে বাষ্পীয় ইঞ্জিন হইল উন্নত হইতে উন্নততর এবং উহা ব্যবহৃত হইতে লাগিল জলে ও স্থলে, বিবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও যানবাহনে। পূর্বে যেখানে ছিল পশুচালিত গাড়ি ও দাঁড়-পালের নৌকা, যাহার গতিবেগ ঘণ্টায় ৭-৮ মাইলের বেশি ছিল না, এখন সেখানে চলিতেছে রেলগাড়ি ও ইঞ্জিনচালিত জাহাজ, যাহার গতিবেগ ঘণ্টায় ক্ষেত্রবিশেষে একশ’ মাইলেরও বেশি। উহাতে যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে পরিবহন ক্ষমতা, তেমনি হ্রাস পাইয়াছে সময়ের অপব্যয়।
বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের ফলে পরম উৎকর্ষ দেখা দিয়াছে শিল্পক্ষেত্রে। ইহাতে যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছে বিবিধ শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন, তেমনই বৃদ্ধি পাইয়াছে আমদানি ও রপ্তানি দ্রব্যের পরিমাণ। সুলভ ও সহজলভ্য হইয়াছে মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। ফলত, মানুষের সমাজজীবনোন্নয়নের মস্তবড় একটি সোপান হইল বাষ্পীয় শক্তির ব্যবহার।
.
# বৈদ্যুতিক শক্তি
সেকালের মানুষের ধারণা ছিল যে, বিদ্যুৎ একটি স্বর্গীয় পদার্থ এবং উহা ব্যবহার করেন দেবতা বা ফেরেশতারা। বিদ্যুৎচমক বা বজ্রপাত সম্বন্ধে মুসলমানগণ বলেন যে, উহা শয়তানের প্রতি ফেরেশতাগণের তীরনিক্ষেপ এবং ‘লা হাওলা অলাকুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহিল আলিওল আজিম’ –এই বাক্যটি উচ্চারিত হইলে সেখানে বজ্রপাত হয় না। পক্ষান্তরে হিন্দুগণ বলিয়া থাকেন যে, দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা বজ্রবাণ তৈয়ারী এবং উহা ব্যবহার করেন দেবরাজ ইন্দ্র, তাহার– শত্ৰুনিপাতের জন্য; ‘জৈমিনিশ্চ সুমন্তু বৈশম্পায়ন এব চ। পুলস্ত্যঃ পুলহো জিফ ষড়েতে বজ্ৰবারকা’ –এই মন্ত্রটি উচ্চারিত হইলে সেখানে বজ্রপাত হয় না। সে যাহা হউক, দেবতাদি বোধ হয় কালসমুদ্রে ডুবিয়া মরিয়াছেন; বর্তমানে বিদ্যুতের স্বত্বাধিকারী হইয়াছে একমাত্র মানুষ।
কাঁচে রেশম ঘষিলে উহাতে যে বিদ্যুৎ জন্মে এবং তাহা যে হাল্কা জিনিষকে আকর্ষণ করে, ইহা অনেকদিন আগে লোকে জানিত। কিন্তু জলপ্রবাহের মতো বিদ্যুতেরও যে প্রবাহ আছে, তাহা বিজ্ঞানীরা জানিয়াছেন মাত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে।
১৭৮৬ খ্রীস্টাব্দে একদিন গ্যালভনি নামক ইতালির একজন বিজ্ঞানী একটি ব্যাঙ মারিয়া তাহার পেশী-স্নায়ু পরীক্ষা করিতেছিলেন। মরা ব্যাঙটি তামার আংটায় ঝুলানো ছিল এবং কাছেই লোহার গরাদ ছিল। হঠাৎ এক আশ্চর্য ঘটনা দেখা গেল। মরা ব্যাঙের দেহ যেমনই গরাদের গায়ে ঠেকিতে লাগিল, অমনি সেইটি জীবিত ব্যাঙের মতো পা ছুঁড়িতে লাগিল। গ্যালভনি তো অবাক। তিনি ভাবিলেন যে, প্রাণীর শরীরে এক রকম বিদ্যুৎ আছে। ধাতু যখন ব্যাঙের দুই অংশে সংযুক্ত করা হইল, তখন সেই বিদ্যুতই তাহার পা সঙ্কুচিত করিল। এই ঘটনা প্রকাশে দেশে বিদেশে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল।
এই সময় ভল্টা নামে একজন মহাজ্ঞানী লোক ছিলেন ইতালিতে। তিনি ঐ বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন যে, শরীরের বিদ্যুৎ মরা ব্যাঙের পা সঙ্কুচিত করে নাই, উহার গায়ে যে তামা ও লোহা ঘেঁয়ানো ছিল, তাহাই বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়াছিল এবং সেই বিদ্যুতই মরা ব্যাঙের পা টানিয়া ধরিয়াছিল। দুই রকম ধাতুকে একত্রে ছোঁয়াইলে যে মরা ব্যাঙ পা ছেড়ে, ভলটা তাহা সকলকে প্রত্যক্ষ দেখাইতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি ব্যাঙকে বাদ দিয়া দুইটি পৃথক ধাতুকে গায়ে গায়ে লাগাইলেন এবং তাহার মধ্যে একটি ধাতু যে ধনবিদ্যুতে (Positive Electricity)। এবং অন্যটি ঋণবিদ্যুতে (Negative Electricity) পূর্ণ হইল, তাহা সকলকে দেখাইলেন।
ভলটা তামা ও দস্তা, এই দুইটি পৃথক ধাতুর কতগুলি চাকতি তৈয়ার করিয়া, তামার উপরে দস্তা ও তাহার উপরে তামা পরে পরে সাজাইয়া একটি যন্ত্র নির্মাণ করিলেন এবং তামা ও দস্তার চাকতির মাঝখানে সালফিউরিক অ্যাসিডে ভিজানো ন্যাকড়া রাখিয়া দিলেন। ইহাতে দেখা গেল যে, উপরকার দস্তায় ঋণবিদ্যুৎ এবং সকলের নিচেকার তামায় ধনবিদ্যুৎ জমিয়াছে। তাহার পর। সব তলাকার তামার চাকতির সঙ্গে উপরকার দস্তার চাকতিকে তার দিয়া সংযুক্ত করায় ঐ তার দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ চলিতে লাগিল। এই যন্ত্রটিকে বলা হয় ‘ভলটার পাইল’।
গ্যালভনির সূচনায় ভলটা তামা, দস্তা ও সালফিউরিক অ্যাসিডের সাহায্যে যে ক্ষীণ বিদ্যুৎ প্রবাহের পরিচয় পাইয়াছিলেন, বর্তমান কালের সব রকম বিদ্যুৎ উৎপাদক কোষ (Battery Cell) তাহারই উপর প্রতিষ্ঠিত। সব রকম বিদ্যুৎ কোষেই থাকে পৃথক দুইটি জিনিষের ফলক এবং একটি সংযোজক বস্তু, আর বাহিরে থাকে ঐ ফলক দুইটিকে সংযুক্ত করিয়া তামা প্রভৃতি ধাতুর তার বা অন্য কিছু। তবে পরে শত শত বিজ্ঞানী নানা চেষ্টায় বিদ্যুতের ক্ষীণ প্রবাহকে প্রবল করিয়া তুলিয়াছেন এবং তদ্বারা মানুষকে ভেল্কিবাজি দেখাইতেছেন। ভলটার নামানুসারে বিদ্যুৎ প্রবাহের বলকে বলা হয় ভোল্ট।
অধুনা বিদ্যুৎ উৎপাদন করিবার পদ্ধতি দুইটি –রাসায়নিক ও যান্ত্রিক। ভলটার কোষে উৎপাদিত বিদ্যুৎকে বলা হয় রাসায়নিক বিদ্যুৎ। ইহাতে বিদ্যুতের পরিমাণ এবং প্রবাহক বল খুব বেশি হয় না। তাই উহা দ্বারা বর্তমান সময়ের ঢাকা, কলিকাতা ইত্যাদির মতো বড় বড় শহরের বিদ্যুতের চাহিদা মিটানো যায় না। উহার জন্য আবশ্যক হয় যান্ত্রিক বিদ্যুৎ। যে যন্ত্রের সাহায্যে যথেচ্ছ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব, তাহার নাম ডাইনামো। একটি সাধারণ ডাইনামো যন্ত্রে যে পরিমাণ বিদ্যুৎ পাওয়া যায়, হাজার হাজার কোষ সাজাইয়াও তাহা পাওয়া সম্ভব নহে। এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করিলেন লিগ শহরের ‘গ্রাম’ নামক একজন বিজ্ঞানী, মাত্র কয়েক বৎসর আগে।
বিদ্যুৎ উৎপাদনের কৌশল জানার পর বিজ্ঞানী মহলে উহা লইয়া নানারূপ গবেষণা চলিতে থাকে এবং কয়েকটি সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীগণ জানিতে পারিলেন যে, কোমল লৌহদণ্ডের উপর তার জড়াইয়া ঐ তারে বিদ্যুৎ চালাইলে লৌহদণ্ডটি চুম্বকত্বপ্রাপ্ত হয়। যে কোনোও চুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ মেরুকে সংযুক্ত করিয়া কতগুলি চৌম্বক বলরেখা বিদ্যমান থাকে। চুম্বকের বলরেখার মধ্যে রাখিয়া কোনো ধাতব তারের বেষ্টনী (কয়েল বা আর্মেচার) নাড়াচাড়া করিলে উহাতে বিদ্যুতের আবেশ হয় (উহাকে আবিষ্ট বিদ্যুৎ বলে)। পরীক্ষায় ইহাও প্রমাণিত হইল যে, চুম্বকের শক্তি ও বেষ্টনীর তারের প্যাঁচের সংখ্যা যতই বাড়ানো যায় এবং বেষ্টনীকে যত দ্রুত ঘুরানো যায়, বিদ্যুতের পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পায়।
উক্ত সূত্র কয়টি অবলম্বনে গ্রাম সাহেব একটি বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র তৈয়ার করিলেন। ঘোড়ার পায়ের নালের মতো একটি বাঁকানো কোমল লোহার গায়ে তামার তার জড়াইয়া উহাতে ক্ষীণ বিদ্যুৎ প্রবাহ চালানো হইলে লৌহটি চুম্বকে পরিণত হইল। অতঃপর বাঁকানো চুম্বকটির মাঝখানে অর্থাৎ চুম্বকের বলক্ষেত্রে বহুপ্যাঁচবিশিষ্ট একটি বেষ্টনী (আর্মেচার) দ্রুত ঘুরাইতে থাকিলে উহাতে খুব শক্তিশালী বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইল। রাসায়নিক বিদ্যুৎ ততক্ষণই পাওয়া যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত কোষে রাসায়নিক ক্রিয়া অব্যাহত থাকে, অতঃপর বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত চুম্বকের বলক্ষেত্রে আর্মেচার ঘুরানো যায়, ততক্ষণ ডাইনামো যন্ত্রে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হইতে থাকে এবং উহা পরিমাণেও হয় কোষের বিদ্যুতের চেয়ে বহুগুণ বেশি। তাই বর্তমানে সব দেশেই ডাইনামো যন্ত্রের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হইতেছে। মূলত সকল ডাইনামো যন্ত্রই গ্রামের উদ্ভাবিত ডাইনামো যন্ত্রের উন্নত সংস্করণ মাত্র।
বিদ্যুৎশক্তির দ্বারা বর্তমান দুনিয়ায় বহু অসাধ্য সাধন করা হইতেছে। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, রেডিও, টেলিভিশন, বাতি, পাখা, মোটর, ট্রাম, এক্সরে ইত্যাদি হইতে শুরু করিয়া রান্না-বান্না, এমনকি ঘর ঝাট দেওয়া পর্যন্ত অসংখ্য কাজ বিদ্যুৎশক্তির দ্বারা সম্পন্ন করা হইতেছে। বর্তমান জগতের যাবতীয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যে বিদ্যুতের ক্ষেত্র সুবিশাল। বিশেষত বিদ্যুৎভিত্তিক যাবতীয় আবিষ্কারগুলিই অতিশয় আশ্চর্যজনক, বলিতে হয় অলৌকিক। বিদ্যুৎশক্তি মানুষকে পৌঁছাইয়া দিয়াছে এক যাদুর রাজ্যে।
.
# পারমাণবিক শক্তি
মানুষ আজ পর্যন্ত প্রকৃতির গর্ভে যত রকম শক্তির সন্ধান পাইয়াছে, তন্মধ্যে পারমাণবিক শক্তি অতুলনীয়। ইহা মানবকল্যাণের অসংখ্য সম্ভাবনায় ভরপুর। সামান্য কয়েক বৎসরের মধ্যে বহুবিধ জনহিতকর কাজে ইহার ব্যবহার শুরু হইয়াছে এবং এই শক্তিটির সাহায্যে মানুষের গ্রহান্তরে গমনের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। কিন্তু নাগাসাকি ও হিরোশিমার ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটিবার নিশ্চয়তাবিধান এখনও হয় নাই। আজও কোনো কোনো দেশের ভূগর্ভে বা সাগরবুকে পারমাণবিক বোমা ফাটার শব্দ কানে আসিতেছে। শান্তিবাদীরা ইহাকে যেমন সৃজনাত্মক কাজে ব্যবহারের জন্য প্রকাশ্যে চেষ্টা চালাইতেছেন, তেমন সাম্রাজ্যবাদীরা ইহার ধংসাত্মক শক্তির উৎকর্ষ সাধনের জন্য গবেষণা চালাইতেছেন গোপনে।
পারমাণবিক শক্তিটির প্রথম সাক্ষাত মেলে পরম বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের বিখ্যাত আপেক্ষিক। তত্ত্বের মাধ্যমে (১৯০৫)। তিনি বলিলেন যে, শক্তির সংহতিতে হয় জড়ের উৎপত্তি এবং জড়ের ধংসে হয় শক্তির উদ্ভব। অর্থাৎ পদার্থ ও তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি আসলে একই জিনিষ। তিনি সূত্র করিলেন –E = Mc2।
আমরা জানি যে, ইলেকট্রন-প্রোটনাদি শক্তিকণিকার সংখ্যার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন জাতীয় পরমাণু তথা মৌলিক পদার্থের রূপায়ণ। শক্তিকণিকাগুলির প্রত্যেকের স্বকীয় ভর বা ওজন আছে। তাই শক্তিকণিকাগুলির সংখ্যানুপাতে নির্দিষ্ট হয় পরমাণুর ওজন। একটি হাইড্রোজেন পরমাণুতে থাকে ১টি ইলেকট্রন ও ১টি প্রোটন এবং উহার আণবিক ওজন হয় ১.০০৮১৩।[৩৩] হাইড্রোজেনের এই আণবিক ওজনের অর্থ হইল এক জোড়া ইলেকট্রন-প্রোটনের ওজন। একটি হিলিয়ামের পরমাণুতে থাকে ২টি ইলেকট্রন, ২টি প্রোটন ও ২টি নিউট্রন; ইহার আণবিক ওজন হওয়া উচিত ৪.০৩৪১৮। কিন্তু দেখা গেল যে, তাহা না হইয়া একটি হিলিয়াম পরমাণুর ওজন পাওয়া যায় ৪.০০৩৮৪, অর্থাৎ সামান্য কিছু কম। ইহার কারণ কি? এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর কোনো বিজ্ঞানী তখন দিতে পারিলেন না।
বিজ্ঞানীপ্রবর আইনস্টাইন বলিলেন যে, ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন লইয়া হিলিয়াম পরমাণু যখন প্রথম গঠিত হয়, তখন একটুখানি পদার্থ বিনষ্ট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বহু পরিমাণ শক্তি বাহির হইয়া যায়। আইনস্টাইনের অঙ্কের হিসাবে দাঁড়াইল— একটি হিলিয়াম পরমাণুর উৎপত্তির জন্য পদার্থের বিলোপে যে শক্তির উদ্ভব হয়, তাহা তিন কোটি বিভবের (potential) তড়িৎ দ্বারা চালিত একটি ইলেকট্রনের শক্তির সমান। এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানী এডিংটন বলেন যে, সূর্যের অভ্যন্তরস্থ সমস্ত হাইড্রোজেনের শতকরা দশভাগ যদি হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়, তবে তাহাতে যে শক্তির উদ্ভব হইবে, তাহা সূর্যের বর্তমান তেজকে বজায় রাখিতে পারিবে ১০০ কোটি বৎসর।
ঐ সম্পর্কে বিজ্ঞানী অ্যাস্টন বলিয়াছেন, “ভবিষ্যতে কোনো গবেষক যদি পদার্থের অন্তর্নিহিত শক্তিকে এইরূপভাবে মুক্ত করিতে পারেন, যাহাতে উহা মানুষের কাজে আসিতে পারে, তবে মনুষ্য জাতি যে প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী হইবে, তাহা বিজ্ঞানের কল্পনার অতীত। এই শক্তি মুক্ত হইলে, হয়তো উহা মানুষের আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে এবং উহার প্রচণ্ডতা হয়তো নিকটবর্তী যাহা কিছু আছে, সব ধ্বংস করিবে। এইরূপে হয়তো পৃথিবীর সমস্ত হাইড্রোজেন মুহূর্তের মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া শক্তিতে পরিণত হইবে এবং তাহা হইলে এই পরীক্ষার সাফল্যে আমাদের পৃথিবী হয়তো ব্রহ্মাণ্ডের একটি নূতন নক্ষত্ররূপে প্রকাশিত হইবে।”
বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকের আইনস্টাইনের সূত্র ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের কল্পনাসমূহ পরবর্তী বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে বাস্তব রূপ পাইল কয়েক বৎসরের মধ্যেই। জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশের ও কানাডার বহু বিজ্ঞানীই পরমাণু ভাঙ্গিয়া উহার। শক্তি সংগ্রহের জন্য নানারূপ গবেষণা করিতে থাকেন এবং বিজ্ঞানী অটোহান ও স্ট্রাসমান পরমাণু ভাগিতে সক্ষম হন। এই সময়টিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা হয় এবং হিটলারের স্বেচ্ছাচারিতায় উত্ত্যক্ত হইয়া জার্মানি, ইতালি, পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরি ইত্যাদি হিটলারের প্রভাবাধীন দেশসমূহের নীলস্ বোর, এনরিকো ফার্মি, ইউজিন ওয়াইগনার, হান, মাইটনার, স্ট্রাসমান ও আইনস্টাইন প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা বিজ্ঞানী স্বদেশ ত্যাগ করিয়া যুক্তরাষ্ট্রে চলিয়া যান। যুক্তরাষ্ট্র সরকার নবাগত ইউরোপীয়ান বিজ্ঞানীগণকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং আবশ্যকীয় অর্থ ও মাল-মশলা দ্বারা পারমাণবিক শক্তি উন্মোচনে তাহাদিগকে যথাযোগ্য সাহায্য করিতে থাকেন।
ইতালির বিজ্ঞানী ফার্মির পরিচালনায় তত্ৰত্য দেশী ও বিদেশী বিজ্ঞানীগণের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টেডিয়ামের একটি স্কোয়াশ কোর্টে ইউরেনিয়ামের পরমাণু ভাঙ্গিয়া পারমাণবিক শক্তি উৎপন্ন সাধ্যায়ত্ত হয় ১৯৪২ সালের ২ ডিসেম্বর।
পারমাণবিক শক্তি আবিষ্কৃত হইলে বিজ্ঞানীগণ মনোনিবেশ করেন পারমাণবিক বোমা তৈয়ার করিতে। আমেরিকার ওপি, ইতালির ফার্মি ও সেগ্রি, ডেনমার্কের নীলস বোর, বৃটিশ মিশনের নেতা শ্যাডউইক প্রমুখ বিশ্বের সেরা বিজ্ঞানী ও তাহাদের সহকর্মীদের সমবেত গবেষণার ফলে অচিরেই তাঁহারা পারমাণবিক বোমা তৈয়ার করিতে সক্ষম হইলেন –নিউ মেক্সিকোর লস আলাম-এ।
পারমাণবিক বোমা তৈয়ার হইলে ১৯৪৫ সালের জুলাই মাসে উহার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো হয় লস আলামস হইতে দুইশত মাইল দূরে মেক্সিকোর আলমো গোর্ডো মরুবক্ষে। ট্রিনিটিতে। ইহাই দুনিয়ার সর্বপ্রথম পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ।
পারমাণবিক বোমার কার্যকর ব্যবহার হইল জাপানের নাগাসাকি ও হিরোশিমা নিবাসী হতভাগ্য মানুষদের প্রাণের উপর, আগস্ট ১৯৪৫-এ। শুধু মানুষই বা বলি কেন, বাদ গেল না পশু, পাখি, কীট-পতঙ্গ এবং জলজন্তুরাও। নিমেষে ধংস হইল অসংখ্য প্রাণী।
পারমাণবিক বিস্ফোরণের সময়ে যে সব তেজস্ক্রিয় রশ্মি বাহির হইয়া আসে, তাহা জীবদেহে। নানারূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এই সম্বন্ধে জাপানের বিজ্ঞানী ডাক্তার মাসাও সুজুকি বলিয়াছেন, “আণবিক পরীক্ষাকার্য এখন বন্ধ করে দিলেও, যা বিস্ফোরণ এ পর্যন্ত হয়েছে, তার ফলেই ২৬ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৫০ হাজার লোক লিউকেমিয়া রোগের কবলে পতিত হবে।” তেজস্ক্রিয়, রশিমালা প্রথমত জীবদেহে ঢুকিয়া রক্তের শ্বেত কণিকার সংখ্যা বাড়াইয়া তোলে এবং লোহিত কণিকাগুলি নষ্ট করিয়া দেয়, ফলে রক্তশূন্যতাজনিত পূর্বোক্ত লিউকেমিয়া রোগ দেখা দেয় ও কোনো কোনো কোষ মারাও যায়। রুগ্ন কোষগুলির বংশবৃদ্ধির ফলে ক্যানসার বা কর্কট রোগ ও চক্ষুর ছানি রোগ দেখা দেয়।
আমরা জানি যে, জীবের জন্মমুহূর্তে থাকে একটি মাত্র জীবকোষ (জননকোষ) এবং তাহাতে ৪৬টি ক্রোমোসোম। এই ক্রোমোসোমে আবার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম একটি পদার্থ থাকে, যাহাকে বলা হয় জীন। এই জীনগুলিই হইল জীবের বংশগতির বৈশিষ্টের নিয়ামক। পারমাণবিক বিস্ফোরণের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ এই জীনগুলির বিশেষ ক্ষতি করে। কোনো স্ত্রীলোক বিকিরণাহত হইলে তাহার সন্তানোৎপাদিকাশক্তি রহিত হইয়া যায় বা কোনো কোনো অবস্থায় গর্ভপাত হয়, কোনো কোনো সময়ে পুরুষেরাও বন্ধ্যাত্ব লাভ করে।
আবার কোনো কোনো সময় তেজস্ক্রিয় রশ্মির ছোঁয়ায় জীনগুলির বিশেষ পরিবর্তন হয়। বিজ্ঞানী স্লেটিস-এর মতে, এই পরিবর্তন বংশানুক্রমে চলিতে থাকে এবং পরিবর্তিত জীনধারী দম্পতির জন্মে অপূর্ণ, অপরিণত ও স্বল্পায়ু সন্তান।
পরম সুখের বিষয় এই যে, বর্তমানে প্রায় সকল রাষ্ট্রই পারমাণবিক মহাশক্তিকে মানবকল্যাণে নিয়োজিত করার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে এবং বিজ্ঞানীগণ কৃষি, চিকিৎসাদি নানা ক্ষেত্রে ইহার ব্যাপক ব্যবহারের গবেষণা চালাইতেছেন। বিজ্ঞানীদের কাছে এখন আর অসম্ভব বলিয়া বেশি কিছু নাই। এই পারমাণবিক মহাশক্তির দ্বারা হয়তো একদিন সম্ভব হইবে মেরু অঞ্চলকে উত্তপ্ত এবং মরু অঞ্চলকে শীতল ও উর্বরা করিয়া উভয়ত প্রাণীবাসের সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করা, জীবকোষের স্বাভাবিক ক্ষয় রোধ বা পূরণ করিয়া জীবকে অমর বা দীর্ঘায়ু করা এবং অনুরূপ আরও অনেক কিছু; হয়তোবা প্রাণসৃষ্টিও।
পারমাণবিক শক্তি একটি মহাশক্তি। শত শত বিজ্ঞানী আজ ব্যস্ত রহিয়াছেন এই শক্তিসমুদ্র মন্থনে। সমুদ্রমন্থনের একটি পৌরাণিক আখ্যান মনে পড়িল। আখ্যানটি এইরূপ — মহর্ষি দুর্বাসার শাপে দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীহীন হইলে লক্ষ্মী সমুদ্রগর্ভে গিয়া বাস করেন। তাহাতে ত্রিলোক শ্রীভ্রষ্ট হয়। পরে ব্রহ্মার উপদেশে দেবগণ মন্দার পর্বতকে মন্থনদণ্ড এবং বাসুকিকে মন্থনরঙ্কু করিয়া সমুদ্রকে মন্থন করিতে থাকেন। এইরূপ মথিত হইলে সমুদ্র হইতে লক্ষ্মী, চন্দ্র, পারিজাত, ধন্বন্তরী, ঐরাবত হস্তী, উচ্চৈশ্রবাঃ অশ্ব প্রভৃতি ও অমৃত উত্থিত হয়। দেবতারা উহা ভাগ করিয়া লন ও অমৃত পান করিয়া অমর হন।
মন্থন শেষ হইলে মহাদেব পুনরায় সমুদ্র মন্থনে প্রবৃত্ত হন এবং তাহাতে ভীষণ হলাহল (বিষ)-এর উৎপত্তি হয়। সেই বিষ এতই অত্যুগ্র যে, ধরিত্রীর কোথায়ও উহা রাখিলে, বিষের জ্বালায় সেই স্থান জ্বলিয়া-পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইবে। অগত্যা মহাদেব স্বয়ং উহা পান করিলেন। কিন্তু গলাধঃকরণ করিলেন না, কণ্ঠে ধারণ করিলেন; তাহাতে তাহার কণ্ঠ হইল নীলবর্ণ। তাই মহাদেবের এক নাম নীলকণ্ঠ।
বর্তমান জগতের বিজ্ঞানীদেবগণ পারমাণবিক শক্তিসমুদ্র মন্থন করিয়া অমৃত উৎপন্ন করিলে পৃথিবী হইবে মানুষের অমরাপুরী, না হইলেও শান্তিনিকেতন। কিন্তু মহাদেব বিজ্ঞানীরা হলাহল উৎপন্ন করিলে, উহার জ্বালায় পৃথিবী জুলিয়া পুড়িয়া হইবে অগ্নিকুণ্ড বা নরকপুরী, যাহাকে বিজ্ঞানী অ্যাস্টন বলিয়াছেন ‘জ্বলন্ত নক্ষত্র’। উহাকে নীলকণ্ঠের মতো আয়ত্তাধীনে আনিবার ক্ষমতা বিজ্ঞানী। মহাদেবদের হইবে কি?
————
২৯. প্রাচীন মিশর, শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৪৮।
৩০. পৃথিবীর ইতিহাস, দেবীপ্রসাদ, পৃ. ১৯৮, ১৯৯।
৩১. প্রাচীন ইরাক, শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৫, ৬।
৩২, প্রাচীন ইরাক, শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ১০।
৩৩. বিশ্বের উপাদান, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, পৃ. ৪২।
১৪. সংস্কার ও কুসংস্কার সৃষ্টি
সংস্কার ও কুসংস্কার সৃষ্টি
প্রত্নতত্ত্ব ও নৃতত্ত্বের সহায়তায় যে মানবেতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে জানা যায় যে, মানুষের জাতিগত জীবনের শৈশবে মানুষ ও ইতর জীবের আহার-বিহার ও মনোবৃত্তির বিশেষ কোনো পার্থক্য ছিল না। সভ্যতার উষালোকপ্রাপ্তির সাথে সাথে পার্থক্যটি প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। তখনকার দিনে যেমনই চলিয়াছিল পশুবৃত্তি দূরীকরণ অভিযান, অর্থাৎ মানুষের সমাজ সংস্কার, আবার তেমনই উহার সহগামী হইয়া চলিয়াছিল শত শত কুসংস্কার। সেইদিনের মানুষের নিছক কল্পিত বিষয় বা কাহিনীগুলি পরবর্তী মানুষের মনে এমনই গভীরভাবে দাগ কাটিয়াছে যে, হাজার হাজার বৎসর পরেও কতক মানুষ ঐগুলিকে ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে।
মানব সভ্যতার মধ্যযুগে গ্রীস, মিশর, ব্যাবিলন, চীন ও ভারতাদি অপেক্ষাকৃত উন্নত দেশসমূহে চলিয়াছিল মানুষের কল্পনাপ্রসূত নানাবিধ জপ, তপ, হোম, বলি ও নানাবিধ ক্রিয়ানুষ্ঠানাদি কুসংস্কারের প্রবল বন্যা এবং উহাই ছিল সেইদিনের মানুষের ধর্ম। ধর্ম তখনও স্বতন্ত্র রূপ লইয়া মানব সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। বলা বাহুল্য যে, সেইদিনের কোনো। ক্রিয়ানুষ্ঠানাদিতে অবশ্যকরণীয় বলিয়া কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। মানুষ তাহার স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই প্রকৃতির নানারূপ শক্তির স্তব-স্তুতি করিত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া স্বাধীনভাবে। এইটা কর, ওইটা করিতে হইবে’ –এই বলিয়া কোনো চাপ ছিল না কোনো ব্যক্তির উপরে।
কালক্রমে যখন অঞ্চলবিশেষের সমাজপতিগণ কতক পূর্বপ্রচলিত ও কতক স্বকল্পিত ক্রিয়ানুষ্ঠানাদিকে অবশ্যকরণীয় বলিয়া প্রচার করিলেন, তখন হইতে তৈয়ারী হইল নিত্য নৈমিত্তিক কর্মতালিকা বনাম ‘ধর্ম’ নামের সূচনা।
ধর্মবেত্তারা সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন কুসংস্কার বর্জন করিতে। তাই দেখা যাইতেছে যে, যে ধর্ম অপেক্ষাকৃত আধুনিক, সেই ধর্ম কুসংস্কারমুক্ত এবং যে ধর্ম পুরাতন, সেই ধর্ম কুসংস্কারে ভরপুর।
বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, আমরা বাস করিতেছি বিরাট এক বায়ুচাপের মধ্যে, যে চাপে পাথরাদি গুড়া হইয়া যাইতে পারে। কথাটি সত্য। কিন্তু আমরা তাহা টের পাইতেছি না। কেননা আমাদের শরীরের বাহিরে যেমন বায়ু আছে, ভিতরেও তেমন বায়ু আছে; ভিতর ও বাহিরের বায়ুর চাপে ঐ চাপ কাটাকাটি হইয়া যায়। বিশেষত জন্মাবধি বায়ুচাপে বাস করিয়া ঐ চাপ হইয়াছে আমাদের। অভ্যাসাগত। কাজেই আমরা অনুভব করিতে পারতেছি না যে, বায়ুর চাপ আছে।
বায়ুচাপের মতোই মানুষের অভ্যাসাগত কুসংস্কার। দূর অতীতের ধর্মবেত্তারা ছিলেন নানাবিধ কুসংস্কারপূর্ণ সমাজের বাঁশিন্দা। তাহাদের ভিতর ও বাহিরে ছিল কুসংস্কার এবং জন্মাবধি কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে বাস করিয়া কিছু হইয়াছিল গা-সহা অভ্যাস। তাই অনেক ধর্মবেত্তাই কু সংস্কার কি ও কোনটি, তাহা অনুধাবন করিতেই পারেন নাই। কাজেই কুসংস্কার বর্জনের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কতক ধর্মবেত্তা বহুক্ষেত্রে ঝোঁপ কাটিয়া জঙ্গল রোপণ করিয়া গিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, কোনো কুসংস্কারই কুসংস্কার বলিয়া সর্বস্তরের লোকের কাছে স্বীকৃতি লাভ করে না।
কুসংস্কার কি, অল্প কথায় ইহার উত্তর হইল, যুক্তিহীন বিশ্বাস বা অসার যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত মতবাদে বিশ্বাস; এক কথায় –অন্ধবিশ্বাস। যেখানে কোনো বিষয় বা ঘটনা সত্য কি মিথ্যা, তাহা যাচাই করিবার মতো জ্ঞানের অভাব, সেখানেই কুসংস্কারের বাসা। অসভ্য, অর্ধসভ্য, অশিক্ষিত ও শিশু মনেই কুসংস্কারের প্রভাব বেশি। কিন্তু কুসংস্কার এত ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া আছে যে, সম্পূর্ণ কুসংস্কারমুক্ত মানুষ অল্পই পাওয়া যায়। যাহারা নিজেদের কুসংস্কারমুক্ত বলিয়া গর্ববোধ করেন, হয়তো কোনো না কোনো রূপে তাহাদের ভিতরেও কিছু না কিছু কুসংস্কার লুকাইয়া থাকিতে পারে বা আছে।
শিশুমনে কুসংস্কারের বীজ ছড়ায় তাহাদের মাতা-পিতা ও গুরুজন, নানারূপ দেও, পরী ও ভূতের গল্প বলিয়া। যদিও বাস্তব জগতে ঐগুলির কোনো অস্তিত্ব নাই, তথাপি একদল মানুষ উহা বিশ্বাস করে ও তাহাদের সন্তান-সন্ততি বা শিষ্যাদির মধ্যে উহার বীজ ছড়ায়। কেননা ঐ সকল অলীক কাহিনী শিশুমনেই দাগ কাটে বেশি।
এমন একটি যুগ ছিল, যখন মানুষ ছিল তাহার জাতিগত জীবনে শিশু। সেই মানব সভ্যতার শিশুকালে তৎকালীন মোড়ল বা সমাজপতিগণ যাহা বলিতেন, জনসাধারণ তাহা অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস ও মান্য করিত; তা বাক্যটি যতই অদ্ভুত হউক না কেন। বর্তমান কালেও কোনো কোনো মহলে দেখা যায়– সত্য-মিথ্যার বিচার নাই, গুরুবাক্য শিরোধার্য। এইখানে আমরা ঐরূপ কতিপয় গুরুবাক্যের অবতারণা করিব, ইহার কোটি সংস্কার এবং কোটি কুসংস্কার, তাহা যাচাই করিবেন সুধী পাঠকবৃন্দ।
.
# দেবতা
হয়তো কোন দেশের কোনো সমাজপতি কল্পনা করিলেন যে, সূর্যের বদৌলতে আমরা তাপ পাই, আলো পাই, বাগান বা ক্ষেতের ফসল পাই এবং উহার দ্বারা আরো কত রকমে উপকৃত হই, সুতরাং উহাকে তুষ্ট না রাখিলে চলে না। তিনি শুরু করিলেন সূর্যের স্তব-স্তুতি, আর জনসাধারণ উহা মানিয়া লইল এবং আরম্ভ হইল সূর্যপূজা। মেক্সিকোর আদিম অধিবাসীরা তো সূর্যের নামে নরবলি প্রথারই প্রচলন করিয়াছিল এবং হাজার হাজার বৎসরে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন নষ্ট হইয়াছে উহাদের সূর্যদেবকে তুষ্ট করার জন্য। দেব-দেবী বা ঈশ্বরের নামে নরবলির বদলে পশুবলির প্রথা প্রায় সব দেশেই আজও প্রচলিত আছে।
শুধু মেক্সিকোতেই নহে, অন্যান্য দেশেও নরবলি প্রথার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহুদিদিগের মধ্যে জাভে-এর তৃপ্তির জন্য নরবলি দেওয়ার প্রচলন ছিল। জজদের যুগে দেখা যায় নবী শামুয়েল বন্দী রাজা আগাগকে প্রভুর নামে স্বহস্তে বলি দিয়াছিলেন (Samuel 15), জেফত তাহার কন্যাকে বলি দিয়া যজ্ঞে আহুতিদান করিয়াছিলেন (Judges II) এবং হজরত ইব্রাহিম তাঁহার পুত্রকে কোরবানি দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ভারতেও এক সময়ে নরবলির প্রথা ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের ‘কপালকুণ্ডলা’ গ্রন্থের কাঁপালিক চরিত্রে।
কোনো দেশের কোনো মুরুব্বি ব্যক্তি হয়তো কল্পনা করিলেন যে, সূর্যের কাছে আমরা অশেষ উপকার প্রাপ্ত হই বটে; কিন্তু উহাকে তো আর হাতের কাছে পাই না! সূর্যের প্রায় সকল গুণই পাওয়া যায় অগ্নির মধ্যে, বস্তুত অগ্নি সূর্যেরই প্রতিরূপ। সুতরাং অগ্নিদেবের তুষ্টার্থে তাঁহার জপ-তপ করাই কর্তব্য। আর তাহার ঐ মত মানিয়া জনসাধারণ আরম্ভ করিল অগ্নিপূজা। হিন্দু ও পারসিকদের মতে, অগ্নি অতীব পবিত্র এবং পরম দেবতা।
আদিম মানব সহজ ও সরল মনেই প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির উপাসনা শুরু করিয়াছিল। তাহাদের ঐ সকল উপাসনার মূলে ছিল বাঁচিয়া থাকার কামনা, স্বর্গপ্রাপ্তি নহে। অনুকূল শক্তিসমূহের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও প্রতিকূল শক্তিকে বশ করিবার প্রচেষ্টাই ছিল আদিম মানবদের প্রকৃতিপূজার মূল উদ্দেশ্য। আবার বিরাট ও বিশাল কিছু দেখিলেই তাহার কাছে তাহারা মস্তক অবনত করিত। বিশেষত প্রত্যেক শক্তিকেই কল্পনা করা হইত ব্যক্তিরূপে। উহারা যেন সকলেই মানুষের মতো আকৃতি-প্রকৃতি বিশিষ্ট এবং ইচ্ছাশক্তির অধিকারী। উহারা ইচ্ছা করিলে যেন মানুষের উপকার বা অপকার দুইই করিতে পারে। এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া আদি মানব শুধু সূর্য ও অগ্নিকেই দেবত্ব দেয় নাই, দেবত্ব দিয়াছিল জল, বায়ু, সাপ, কুমির, বাঘ, নদী, সাগর, পাহাড়, নক্ষত্র, মেঘ, বৃষ্টি, ঝঞ্ঝা, বস্ত্র, বটবৃক্ষ এবং কোনো কোনো পশু পাখিকেও।
ঐসব পার্থিব দেবতা ভিন্ন কতগুলি অপার্থিব দেবতারও কল্পনা হইয়াছিল। যেমন– ক্রোধের দেবতা রুদ্র, সাম্যের দেবতা বিষ্ণু, সম্পদের দেবী লক্ষ্মী, বিদ্যাদেবী সরস্বতী ইত্যাদি। আবার কোনো কোনো দেশে মানুষকেও দেবাসনে বসানো হইয়াছে, কোথায়ও মহামানব বা কোথায়ও দেব-অবতাররূপে। যেমন –শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, নমরুদ, ফেরাউন ইত্যাদি (ফেরাউন কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে, উহা রাষ্ট্রীয় উপাধি মাত্র)।
আদিম মানবদের ঈশ্বরকল্পনা ছিল না, কল্পনা ছিল দেবতার। যে তাপ ও আলো দান করে, সে একজন দেবতা; যে খাদ্য দান করে, সে একজন দেবতা; যে বৃষ্টি দান করে, সে একজন দেবতা; এইরূপ– ঝঞ্ঝার দেবতা, বজ্রের দেবতা, মৃত্যুর দেবতা ইত্যাদি অজস্র দেবতা। মনে করা হইত যে, দেবতারা সকলেই এক একটি কার্য নির্বাহ করিয়া থাকেন স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে। কাজেই উহারা প্রত্যেকেই এক একটি বিষয়ের মালিক। অর্থাৎ বিভাগীয় ঈশ্বর (Departmental God) পরবর্তী কালের মানুষ কল্পনা করিল যে, ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন শক্তির মূলে একটি মহাশক্তি আছে, তখন তাহার নাম রাখা হইল বিশ্ব অধিপতি বা পরম ঈশ্বর। কিন্তু দেখা গেল যে, পরম ঈশ্বর তো স্বহস্তে কিছুই করেন না, তবে প্রকৃতির যাবতীয় ঘটনা ঘটে কি রকম? তখন কল্পনা করা হইল যে, যাবতীয় কার্য নির্বাহ ঐ সকল দেবতারাই করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু পরমেশ্বরের হুকুমমতে। দেবতারা সকলেই পরমেশ্বরের নির্দেশমতে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিয়া থাকেন মাত্র। তবে আগের পরিকল্পনাটি একটু পরিবর্তন করা হইল। দেবতারা ছিলেন ৩০-৪০ কোটি বা নির্দিষ্ট সংখ্যক, কিন্তু স্বর্গীয় দূতেরা অসংখ্য। পরমেশ্বর বা একেশ্বর কল্পনার পূর্বে যাহারা ছিলেন। দেবতা, একেশ্বর কল্পনার পরে তাহারাই বনিয়াছেন স্বর্গীয় দূত। প্রাচীন মানবের এই স্বর্গদূত পরিকল্পনাটি পরে স্থান পাইয়াছে কতগুলি ধর্মে।
কোনো কোনো অঞ্চলে কল্পনা করা হইল প্রত্যেকটি রোগের কারণ ও বাহনরূপে এক একটি অপদেবতার। জ্বর, কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি যত প্রকার রোগ আছে, তাহার প্রত্যেকটির পরিবাহক এক একটি অপদেবতাও আছে এবং ঐ সকল রোগের প্রতিকারার্থে নানাবিধ তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাড় ফুঁকেরও প্রচলন হইয়াছিল সেই আদি কালেই, যাহা স্থানবিশেষে এখনও প্রচলিত আছে।
.
# জন্মান্তর
জন্মান্তর কল্পনাটি অতি প্রাচীন। ইহার দুইটি রকমভেদ আছে। যথা –পুনর্জন্ম এবং পুনর্জীবন। হিন্দু ও বৌদ্ধগণ পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। ইহাদের মতে, দেহ নশ্বর, কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর। অর্থাৎ জীবের মুত্যুর পরে তাহার এই পার্থিব দেহ লয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আত্মা লয়প্রাপ্ত হয় না। এই জন্মের ভালো বা মন্দ কর্মানুসারে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট জীবরূপে আত্মা আবার জন্ম লয়। অর্থাৎ মৃত্যুর পর আত্মা নূতন জনমে রাজা বা ভিখারী, চোর বা সাধু অথবা শিয়াল-কুকুর, কীট-পতঙ্গও হইতে পারে। কিন্তু আদিম মানবদের মনে (পরকালে) পাপ-পুণ্যের ফলভোগ-এর কল্পনা ছিল না, ছিল শুধু পুনর্জীবনের আশা। ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় প্রাচীন মিশরীয়দের সমাধিগুলিতে রক্ষিত আসবাবপত্র ও জাঁকজমক দেখিয়া।
ইহুদি ও খ্রীস্টানাদি সেমিটিক জাতিরা জন্মান্তরে বিশ্বাসী নহেন, তাহারা বিশ্বাসী পুনর্জীবনে। তাহাদের মতে, মানুষ মৃত্যুর পর তাহার পূর্বদেহেই কোনো এক সময়ে আবার জীবন ফিরিয়া পাইবে এবং তখন সে তাহার ন্যায় বা অন্যায় কাজের ফল ভোগ করিবে।
পুনর্জীবনের কল্পনাটি বোধ হয় প্রথম জাগিয়াছিল প্রাচীন মিশরীয়দের মনে। কল্পনাটির মূল উৎস ছিল দুইটি –সূর্য ও নীলনদ। মিশর দেশটি সাহারা মরুর অংশবিশেষ। প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থানক্রমে ঐখানে সূর্যের যতখানি প্রতাপ, পৃথিবীর অন্য আর কোথায়ও তত নহে। কাজেই সূর্য মিশরবাসীদের মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল বেশি এবং সূর্যকে লইয়া উহারা জল্পনা-কল্পনাও করিয়াছিল বেশি। তাহারা দেখিয়াছিল যে, এমন প্রচণ্ড প্রতাপশালী সূর্য ভোরে জন্মলাভ করিয়া শৈশব, যৌবন ও বার্ধক্যে পৌঁছিয়া সন্ধ্যায় অস্তাচলে গমন করে, অর্থাৎ উহার মৃত্যু হয়। পরের দিন ভোরে আবার পুনর্জীবন লাভ করিয়া পূর্ববৎ উদিত হয়। ঐরূপ মানুষের জীবনও এই দেহে ফিরিয়া আসিবে– এইরূপ আশা প্রাচীন মিশরীয়দের মনে উঁকি মারিতেছিল।
মিশরীয়দের মনে আর একটি আকর্ষণীয় বিষয় ছিল নীলনদ। মরুময় মিশর দেশকে শস্যশ্যামল করিয়া মিশরবাসীগণকে বাঁচাইয়া রাখে নীলনদ। তাহারা দেখিত যে, বৎসরের একটি নির্দিষ্ট দিনে নীলনদে বান ডাকিয়া জল আসে। শুরুতে জল আসে অল্প অল্প এবং ক্রমে জল বৃদ্ধি পাইয়া প্রবল আকার ধারণ করে, নীলনদের যৌবনজোয়ার মিশর দেশকে ডুবাইয়া দেয়। আবার ক্রমে ক্রমে উহা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া জলশূন্য হইয়া যায়। তখন হয় নীলনদের মৃত্যু। কিন্তু বৎসরান্তে আবার জল আসে, দেশ ভাসে, নীলনদ পুনর্জীবন পায়। নীলনদের এই বার্ষিক জন্ম-মৃত্যুর ঘটনাটি সূর্যের দৈনিক জন্ম-মৃত্যুর ঘটনাটির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ সন্দেহ নাই। কাজেই প্রাচীন মিশরীয়দের মনে ভালোভাবেই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, মৃত্যুর পরে ঐরূপ মানুষও পুনর্জীবন লাভ করিবে।
তাই প্রাচীন মিশরীয়রা শবকে নষ্ট হইতে দিত না, সযত্নে কবর দিত এবং মৃতের আহারের। জন্য খাদ্য-পানীয়, ব্যবহারের জন্য নানাবিধ পাত্র, আত্মরক্ষার জন্য হাতিয়ার ও সুখ-সুবিধার অন্যান্য দ্রব্য কবরে দিত। রাজরাজড়াদের কবরে নাকি দাস-দাসী, পরিজন, পাত্র-মিত্রগণও স্থান লাভ করিত এবং উহার অভাবে ঐসবের মূর্তি বা চিত্র কবরে রাখা হইত। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মিশরে খননকার্যের দ্বারা বহু কবরে ঐসকল প্রাপ্ত হইয়াছেন।
পুনর্জীবনে বিশ্বাসবশত মানবদেহকে অক্ষত রাখার চরম প্রচেষ্টারই ফল মিশরের পিরামিড। গিজার বড় পিরামিডটির মধ্যে যে সকল জিনিসপত্র পাওয়া গিয়াছে, দুই-এক পৃষ্ঠা কাগজে তাহার তালিকা ধরে না। সোনাদানার নানা রকম জিনিস হইতে আরম্ভ করিয়া চেয়ার, টেবিল, খাট-পালক, বাসনকোসন, এমনকি নখ পালিশ করিবার সুন্দর ছোট যন্ত্রপাতি পর্যন্ত ঐ সকল পিরামিডে পাওয়া গিয়াছে। আর পাওয়া গিয়াছে জীবদ্দশায় রাজার যে সমস্ত পাত্র-মিত্র, সভাসদ এবং দাস-দাসী ছিল, তাহাদের মূর্তি। অর্থাৎ জীবদ্দশায় যাহারা রাজার সাঙ্গপাঙ্গ ছিল, তাহাদের অভাবে রাজার যাহাতে কষ্ট না হয়, সেই জন্য জীবন্তের প্রতীক হিসাবে এই মূর্তিগুলি রাজার আশেপাশে রাখা হইত। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, আদিতে ইহাদের জীবন্ত অবস্থাতেই সমাধিস্থ করা হইত।[৩৪]
পণ্ডিতগণের অনুমান যে সত্য, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে প্রাচীন সুমের ও ব্যাবিলোনিয়ার কয়েকটি সমাধিগর্ভে। সাধারণ নাগরিকেরা গর্ত খুঁড়িয়া মৃতকে কবর দিত, তাহার আভরণ, শখের বস্তু, ছোরা, সিলমোহর, ধাতু বা পাথর নির্মিত পাত্র ইত্যাদি সমেত। কিন্তু রাজরাজড়ার সমাধি এক বিরাট কাণ্ড। বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে উর নগরের খননকার্যের ফলে রাজ্ঞী সুব-আদ ও তাঁহার স্বামীর দুইটি সমাধি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার বিশেষ বিবরণ দিয়াছেন প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার লিওনার্ড উলি। বিবরণটি নিম্নরূপ —
“মাটির নিচে প্রস্তুত করা হইয়াছে একটি ইষ্টকনির্মিত সৌধ, সেটি সমাধিগৃহ। তাহার মধ্যে চারিটি কক্ষ। রাজা ও রাণীকে দুইটি কক্ষে সমাধি দান করা হইয়াছে, আর বাহিরের দুইটি কক্ষে এবং প্রবেশপথে পড়িয়া আছে অনেকগুলি নর-নারীর কঙ্কাল, সারিবদ্ধভাবে শায়িত। এক জায়গায় দশটি নারীদেহ রহিয়াছে দুই সারিতে। তাহাদের মাথায় ও কণ্ঠে সোনার ও পাথরের অলঙ্কার। একটি সোনার মুকুট পরা মেয়ের হাতে রহিয়াছে একটি বীণা। সমাধিকক্ষে প্রবেশ করার জুলি পথে একটি রথ, আর রথের উভয় পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে স্বর্ণনির্মিত সিংহমূর্তি, নানা। রকমের কাজ করা। সোনা-রূপার সিংহ ও বৃষের মূর্তিতে রথের চূড়াদেশ সজ্জিত। সম্মুখেই দুইটি গর্দভের ও সিংহের কঙ্কাল আর দূতক্রীড়ার ছক, নানাবিধ অস্ত্র, স্বর্ণ ও তাম্র পাত্র এবং পাথরবাটি। প্রস্তরনির্মিত কক্ষটির প্রান্তদেশে নয়টি নারী, সকলেরই মাথায় রত্নভূষণ, কানে সোনার দুল ও মাকড়ি। মোট ৬৮টি নারীর কঙ্কাল ছিল সমাধিগর্ভে, তাহার মধ্যে ২৮টির মাথায় স্বর্ণালঙ্কার পুরানো।
“রাজা-রাণীর সমাধিগৃহে রত্নভূষণে সজ্জিত স্ত্রীলোক, পুরুষ মানুষ, রথ ইত্যাদি প্রোথিত হইয়াছিল কেন? ইহার অত্যন্ত সহজ উত্তর এই যে, রাজা-রাণীর সঙ্গে তাহাদের পরিচারক পরিচারিকাদেরও সমাধি দেওয়া হইত, যেমন প্রোথিত করা হইত তাহাদের শখের জিনিস, আবশ্যকীয় দ্রব্য। জিনিসের প্রয়োজন হইত ব্যবহারের জন্য, আর দাস-দাসীর প্রয়োজন হইত পরলোকের সেবার জন্য।”[৩৫]
.
# তালমুদিক শিক্ষা
প্রাচীন হিব্রু জাতির মধ্যে কতগুলি রূপকথা-উপকথা বা কাহিনী প্রচলিত ছিল। সেই সব কাহিনীর ব্যক্তি বা স্বর্গদূতগণের নাম হয়তো বাইবেলে আছে, কিন্তু সেই নামের সূত্র ধরিয়া (উপন্যাসের আকারে) কতগুলি পার্থিব ও অপার্থিব প্রাণীদের কল্পিত কাহিনী দীর্ঘকাল ধরিয়া হিব্রুদের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল। কালক্রমে ইহুদি পুরোহিত বা ‘রাবিব’গণ ঐ কাহিনীগুলিকে সংকলন করিয়া বিরাট দুইখানা পুস্তক লেখেন। গ্রন্থদ্বয়ের নাম তালমুদ ও মিদ্রাস। ঐ গ্রন্থ দুইখানি রূপকথা-উপকথার অফুরন্ত ভাণ্ডার এবং কুসংস্কারের পাহাড়। বর্তমান জগতে যত রকম কুসংস্কার প্রচলিত আছে, বোধ হয় যে, ঐ গ্রন্থ দুইখানিই তাহার কেন্দ্র। মুশকিল হইল ঐ জায়গায় যে, তালমুদে বর্ণিত কাহিনীগুলির মূল সূত্র অর্থাৎ ব্যক্তি বা স্বর্গদূতগণের নাম বাইবেলে লিখিত থাকায় কেহ কেহ ঐসব কম্পিত কাহিনী গ্রহণ করিতেছে ধর্মীয় কাহিনী হিসাবে, অর্থাৎ সত্য বলিয়া। তালমুদ গ্রন্থে বর্ণিত তিনটি উপকথার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি।
লিলিথের উপকথা
লিলিথ মানুষের মতোই মাটির তৈয়ারী একজন স্ত্রীলোক। সে প্রথমে শয়তানকে বিবাহ করে ও তাহাকে ত্যাগ করিয়া বিবাহ করে আদমকে। আদমের সহিত তাহার বনিবনা না হওয়ায় সে পলাইয়া যায় এবং আদম ঈশ্বরের কাছে নালিশ করে। ঈশ্বর তিনজন স্বর্গদূত পাঠায় লিলিথকে ধরিয়া আনিবার জন্য। কিন্তু তাহারা তাহা পারে না (সম্ভবত এই সময়ে হাওয়ার সহিত আদমের বিবাহ হয়)। আদম এদন উদ্যান হইতে বিতাড়িত হইয়া হাওয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর লিলিথ আদমের সাথে পুনঃ মিলিত হয় এবং ৩০ বৎসর আদমের ঘর-সংসার করে। এই সময়ে লিলিথের গর্ভে যে সকল সন্তান জন্মে, তাহারা হইল ‘শেদিম’ (Shedim) বা দানব।
স্বর্গদূত প্রতিষ্ঠান
ইহুদিদের মতে স্বর্গদূত তিন শ্রেণীর –সিরাফিম, চিরাবিম ও ওনাকিম। অগ্নি উপাদানে উহাদের দেহ গঠিত। উহাদের নিঃশ্বাসে মনুষ্য দগ্ধ হয় ও কণ্ঠস্বরে মানুষের কর্ণপটাহ বিদীর্ণ হয়। আধা আগুন ও আধা বরফের তৈয়ারী এঞ্জেলও আছে। এই দলের নাম ইসিম। মৃত্যুর এঞ্জেলের চক্ষুদ্বয় আগুনের তৈয়ারী। তাহার দিকে চাহিলেই মানুষ ধরাশায়ী হয়। এঞ্জেল অসংখ্য। চিনিবার জন্য প্রত্যেকের বক্ষে একটি করিয়া চাকতি লাগানো থাকে এবং তাহাতে ঈশ্বরের নামের সাথে লেখা থাকে এঞ্জেলের নাম। এঞ্জেলদের প্রত্যেকের কর্তব্য ঠিক করিয়া দিয়াছেন ঈশ্বর (আদিতে যাহারা ছিল দেবতা, তাহারাই তালমুদে বনিয়াছে স্বর্গদূত)। যথা —
১. আফাত্রিয়েল ইনি মানুষের চিন্তা ও বাক্য স্বর্গে বহন করেন।
২. গালিজুর ঈশ্বরের বাণী পৃথিবীর গোচরে আনেন।
৩. বেননেজ নিয়ন্ত্রণ করেন ঝঙ্কাকে।
৪. বারাকিয়েল নিয়ন্ত্রণ করেন বিদ্যুতকে।
৫. লাইলাহেম নিয়ন্ত্রণ করেন রাত্রিকে।
৬. জোরকামি নিয়ন্ত্রণ করেন শিলাবৃষ্টিকে।
৭. রাশিয়েল নিয়ন্ত্রণ করেন ভূমিকম্পকে।
৮. সালগিয়েল। নিয়ন্ত্রণ করেন তুষারপাতকে।
৯. রাহাব নিয়ন্ত্রণ করেন সমুদ্রকে।
১০. সানডেল ফোন ইনি পৃথিবীর উপরে দাঁড়াইয়া আছেন। ইঁহার মাথা স্বর্গ স্পর্শ করে, ইনি সৃষ্টিকর্তার মহিমার রশ্মিকিরিটী বয়ন করেন (বোধ হয়, ইনি সূর্য)।
১১. রেডিয়াও ইনি বৃষ্টির এঞ্জেল। ইনি স্বর্গের ও পৃথিবীর জলরাশি নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁহার জলদমন্দ্র কণ্ঠস্বর পৃথিবীময় ধ্বনিত হয় (বোধ হয় মেঘগর্জন)।
১২. মেটাট্রোন ইনি পৃথিবী পরিদর্শনের কার্য করেন। ধর্ম ও শাস্ত্রসমূহের সংরক্ষণের ভার হঁহার উপরে। বনি ইস্রায়েলদের মিশর হইতে স্বদেশে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার কাজ ইহাকে অর্পণ করা হইয়াছিল।
ঐ সকল এঞ্জেলদের উপরে বিরাজ করেন কয়েকজন আর্কেঞ্জেল, অর্থাৎ প্রধান এঞ্জেল। যেমন –মাইকেল, র্যাফেল, গ্যাব্রিয়েল, উরিয়েল ইত্যাদি। ইহারা ঈশ্বরের আদেশে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করিয়া থাকেন।
শয়তান ও পতিত দূতগণ
শয়তান ছিল সিরাফিম গোষ্ঠীর একজন আর্কেঞ্জেল। তাহার ইহুদি নাম সামমায়েল। তাহার বারোটি পাখা ছিল। ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করায় শয়তান ও তাহার অনুচরদের প্রতি দণ্ডাদেশ হইল নির্বাসনের। সেই আদেশ তাহারা প্রত্যাখ্যান করিল। তখন ঈশ্বরের দূতগণের সঙ্গে তাহাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল (ইহা পারসিকদের অহুরমজদা ও আহরিমান-এর আখ্যানের অনুরূপ)। স্বর্গদূত বাহিনীর নেতা ছিলেন আর্কেঞ্জেল মাইকেল। শয়তানের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে তিনিই প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। শেষমেশ শয়তান ও তাহার অনুচরদের পরাজয় হইল এবং উহাদের পতন হইল স্বর্গ হইতে নরকে (পৃথিবীতে)। সেই সময় হইতে মানুষের অহিতসাধন ও ঈশ্বরবিরোধী করিয়া তাহাদের বিপথে চালাইয়া লওয়াই হইল শয়তানের একমাত্র ব্রত।
স্বর্গীয় এঞ্জেলদের মতো নরকে (পৃথিবীতে) শয়তানের অনুচর দানবগণও সংঘবদ্ধভাবে একটি প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছিল। দানবগণ ছদ্মআকারে মর্তমানবকে আশ্রয় করিয়া নানা আধি-ব্যাধি সৃষ্টি করে, বিশেষ ক্ষেত্রে মানুষের বশ্যতাও স্বীকার করে এবং আলাউদ্দীনের প্রদীপের দানবের মতো মানুষের কাজেও লাগে। এই দানবগোষ্ঠী চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা –শেদিম, রউখিল, মাজিকিল ও লেলিন। মানুষ ও স্বর্গদূত, এই উভয় জাতির গুণ বিদ্যমান আছে এই দানবদের মধ্যে। মানুষের মতো তাহারা আহার-বিহার ও বংশবৃদ্ধি করে, মানুষের মতোই তাহাদের মৃত্যু হয়, অথচ এঞ্জেলদের মতো তাহাদের পাখা আছে। গগনে বিহার করিতে পারে (ইহা দেও-পরীর কল্পনার উৎস)। দিব্যদৃষ্টিতে ভবিষ্যতকে দেখিতে পায়। ইচ্ছামতো মানুষ বা অন্য প্রাণীর রূপ ধারণ করিতে পারে এবং নিজে অদৃশ্য থাকিয়া অন্যকে দেখিতে পারে। পৃথিবীতে তাহাদের বাসস্থান মরু-কান্তার, জলাভূমি, শ্মশান ইত্যাদি। বাঁধা বস্তু বা সিলমোহর দেওয়া কোনো জিনিসের উপর তাহাদের প্রভাব নাই। ঈশ্বরের নাম উচ্চারণমাত্র উহারা সেখান হইতে পলাইয়া যায় ইত্যাদি।[৩৬]
বলা বাহুল্য যে, তালমুদীয় আবহাওয়া হইতে কোনো দেশ বা কোনো জাতিই সম্পূর্ণ মুক্ত নহে।
.
# ভূত
মধ্যযুগে পূর্ব ইউরোপীয় ইহুদি ধর্ম হইয়াছিল ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানব ও ডাকিনী-যোগিনীর বাসা। ইহুদিদের মধ্যে ভূতে পাওয়ার বিশ্বাস বিশেষভাবে প্রসার লাভ করিয়াছিল। ঐ সকল ভূত বা দানবদের বলা হইত দিল্লুক (Dibbuk)। উহারা নাকি মানুষের দেহকে আশ্রয় করিত এবং যাহার উপর চাপিত, তাহার ব্যক্তিত্ব একেবারেই লোপ পাইত। নানাবিধ তন্ত্র-মন্ত্র, তাবিজ-কবচ এবং ওঝার ঝাড়-ফুঁক উদ্ভাবন ও প্রচলন করিয়াছিল সেই কালের ইহুদিরা। ঐগুলি এখনও প্রচলিত রহিয়াছে অনুন্নত দেশগুলিতে।
খ্রীস্টান জগতে ভূতে পাওয়া সম্বন্ধে ধারণা ছিল আরও অদ্ভুত। তাহারা ভূতে পাওয়া রোগী দুনিয়ায়ই রাখিত না, মারিয়া ফেলিত। তবে এখন আর মারে না।
ভূত-প্রেত বা গন্ধর্ব মানুষকে আশ্রয় করে, এই বিশ্বাস ভারতীয় বৈদিক যুগেও ছিল। তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় বৈদিক সাহিত্যে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে দেখা যায়, পাতঞ্জল কাপ্যের এক কন্যা গন্ধর্বগৃহীতা (আবিষ্টা) হইয়াছিল।
ঘটনা সাধারণত দুই জাতীয়– লৌকিক এবং অলৌকিক। আবার অলৌকিক ঘটনার কতগুলিকে বলা হয় ঐশ্বরিক এবং কতগুলিকে ভৌতিক। যে সমস্ত ঘটনার কারণসমূহ সাধারণত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহাকে বলা হয় লৌকিক এবং যাহা ইদ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তাহাকে বলা হয় ঐশ্বরিক বা ভৌতিক।
রোগও দুই জাতীয় –শারীরিক ও মানসিক। কলেরা, বসন্ত ও জ্বরাদি রোগসমূহ শারীরিক; ইহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। উন্মাদাদি রোগসমূহ মানসিক। ইহার কারণাবলী ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা সহজবোধ্য নহে। তাই এক শ্রেণীর মানুষ উহাকে বলে ভৌতিক অর্থাৎ ভূতের আশ্রয়।
ভূতে পাওয়া রোগীরা কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, কখনও নাচে বা গান গায়; কেহ আবোলতাবোল বকে, কেহবা গুম হইয়া বসিয়া থাকে ইত্যাদি।
ভূতে পাওয়া রোগ– ১. শিক্ষিত অপেক্ষা অশিক্ষিতের মধ্যে বেশি, ২. শহর অপেক্ষা গ্রামাঞ্চলে বেশি, ৩. পুরুষ অপেক্ষা নারীর বেশি এবং ৪. শিশু ও বৃদ্ধ অপেক্ষা যুবক-যুবতী বা মধ্যবয়সীদের মধ্যে বেশি দেখা যায়।
রোগের কারণ– ১. সুশিক্ষিত ব্যক্তিরা কুসংস্কারমুক্ত এবং অশিক্ষিতরাই নানাবিধ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। উহারা যে কোনো রোগ বিশেষত মানসিক রোগের দায় কথায় কথায় দেও, পরী বা ভূতের মাথায় চাপাইয়া থাকে। ২. সাধারণত শহর হইতে পল্লী অঞ্চলে অশিক্ষিতের সংখ্যা বেশি। উহারা যে কোনো মানসিক বিকৃতিকে ‘ভূতের দৃষ্টি’ বলিয়া, এমনকি কলেরা-বসন্তকেও ‘ওলা’ এবং শীতলা’র উৎপাত বলিয়া মনে করে। ৩. মনোবিজ্ঞানী ফ্রয়েডের মতে উন্মাদ রোগ অধিকাংশই প্রণয় বা কাম ঘটিত। উহার মূল কারণ হইল যৌনমিলনে বিফলকাম হওয়া। উহার ডাক্তারী নাম নিম্ফম্যানিয়া বা কামোন্মাদ। কামঘটিত ব্যাপারে পুরুষদের অপেক্ষা নারীরাই বিফলকাম হয় বেশি, তাই উহাদের কামোন্মাদ রোগ বনাম ভূতের দৃষ্টিও বেশি, বিশেষত যৌবনে। ৪. অনেক চিকিৎসকের মতে রমণীদের মাসিক ঋতুর বা প্রসবান্তে জরায়ুর গোলমালের জন্য অনেক ক্ষেত্রে উন্মাদ রোগ জন্সিয়া থাকে। রমণীদের শৈশব ও বার্ধক্যে উহার কোনোটিই থাকেনা, থাকে যৌবনে। কাজেই মধ্যম বয়সী রমণীদের উন্মাদনা বা ভূতের আশ্রয়ও বেশি। এতদ্ভিন্ন নানাবিধ কারণে মানুষের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিয়া থাকে। পল্লী অঞ্চলে ঐগুলির দায়ও ভূতের মাথায় চাপানো হয়। বস্তুত দেও, পরী, ভূত ইত্যাদি নামের কোনো জানোয়ার দুনিয়ায় নাই।
.
# শপথ
মহাপ্রবরদের যুগে একটি প্রথা ছিল এই যে, যদি কোনো ব্যক্তির শপথ করিবার আবশ্যক হইত, তবে যাহার কাছে শপথ করা হইত, শপথকারী তাহার লিঙ্গ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞাপূর্বক শপথ করিত। (জেনেসিস ২৪; ৯, ৪৭ )
ঐরূপ কোনো কিছু স্পর্শ করিয়া শপথ করিবার রেওয়াজ এখনও আছে। শপথ করিতে হইলে এইদেশের হিন্দুরা স্পর্শ করেন তামা ও তুলসী, মুসলমানে পবিত্র কোরান এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে স্পর্শ করেন পুত্রের মাথা।
.
# জাদু
আদিম মানুষদের মধ্যে শত্ৰুনিপাতের উপায় হিসাবে কতগুলি প্রক্রিয়ায় বিশ্বাস ছিল, উহাকে বলা হয় জাদু। জাদু কথাটিকে ইংরাজিতে বলে ম্যাজিক। কিন্তু আলোচ্য জাদু কথাটির ইংরাজি একটু অন্য রকম। জাদুবিশ্বাস দুই রকম। উহার ইংরাজি নাম –কটেজিয়াস ম্যাজিক ও ইমিটেটিভ ম্যাজিক।
মনে করা যাক, কোনো শত্রুকে জাদু দ্বারা বধ করিতে হইবে। এখন উহার ব্যবস্থা হইল– শত্রুর চুল, নখ বা কাপড়ের খুঁট কাটিয়া আনিয়া উহা আগুনে পোড়াইয়া ফেলা। ইহাতে শত্রু জ্বলিয়া-পুড়িয়া মরিবে। এইরূপ বিশ্বাসকে বলা হয় কনটেজিয়াস ম্যাজিক।
আবার শত্রুর একটি মূর্তি তৈয়ার করিয়া উহার গায়ে একটি তীর বিদ্ধ করা হইল এবং মনে করা হইল যে, ইহাতে শত্ৰুটির দেহ ধীরে ধীরে ক্ষয় পাইয়া শেষে সে মারা যাইবে। এইরূপ বিশ্বাসকে বলা হয় ইমিটেটিভ ম্যাজিক।
উক্ত দুই প্রকার ম্যাজিক বা জাদুর প্রচলন হাল আমলেও এইদেশের গ্রামাঞ্চলে কিছু কিছু আছে। উহার গ্রাম্য নাম বাণ বা টোনা।
.
# ইন্দ্রজাল
পুরাকালে এক রকম বিদ্যা ছিল ইন্দ্রজাল। উহাতে ছিল নানারূপ ভূত-প্রেত ও ডাকিনী-যোগিনীর কল্পনা, যথা –উগ্রচণ্ডী, ভৈরবী, বাসুকি ইত্যাদি; নানারূপ বিদঘুঁটে পদার্থ, যথা –চিতার কয়লা, দাঁতের ময়লা, মরা মানুষের মাথার খুলি ইত্যাদি এবং নানাবিধ তন্ত্র-মন্ত্র। মারণ, স্তম্ভন, উচাটন ও সম্মোহন ইত্যাদি কাজের জন্য দরকার হইত ভিন্ন ভিন্ন সময়ের, যথা –কালীসন্ধ্যা বা অন্ধকার গভীর রজনী, শনি বা মঙ্গল বার, অমাবস্যা তিথি ইত্যাদি; ভিন্ন ভিন্ন স্থান, যথা –তেপথা, চিতাখোলা, বিজন বন ইত্যাদি এবং ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র ও আসন। সাধক যথাবিহিত আসনে উপবেশনপূর্বক যথারীতি অনুষ্ঠান পালন করিলেই ঈপিত ফললাভ হইয়া থাকে। এই সবে বিশ্বাসের আমেজ এখনও কিছু কিছু আছে।
হাজার হাজার বৎসর পূর্বে, ধাতুযুগের প্রারম্ভে আসিরিয়া দেশে একটি অদ্ভুত আচার প্রচলিত ছিল। এখন আমরা ধাতুদ্রবণকে মনে করি যে, উহা একটি বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা বা রাসায়নিক ক্রিয়া। কিন্তু সেই যুগের আসিরিয়াবাসীদের ধারণা ছিল অন্য রকম। তাহারা যখন দেখিত যে, দুইটি ধাতুপদার্থ একত্রে গলাইলে একটি অভিনব পদার্থের সৃষ্টি হয় এবং পাথরাদি হইতে লৌহাদির উৎপত্তি হয়, তখন তাহারা উহাকে মনে করিত ইন্দ্রজাল বলিয়া। এই বিদ্যার অধিকারী সকলে নহে, শুধু একশ্রেণীর কারিগর। যেমন আমাদের দেশের কামার, কুমার ইত্যাদি শিল্পীরা। এইটি ছিল একটি গুপ্তবিদ্যা। কতগুলি রহস্যাত্মক ঐন্দ্রজালিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে এই বিদ্যাটি জড়িত ছিল। আসিরিয়ার কয়েকটি শিলালিপিতে এই অনুষ্ঠানগুলির বিবরণ পাওয়া যায়। অত্যন্ত বীভৎস রকমের অনুষ্ঠান। কার্য আরম্ভের পূর্বে নবগভিনী রমণীর ও তাহার গর্ভস্থ সূণের রক্ত দিয়া অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইত। বর্তমানে অনেক আদিম জাতির কারিগরেরা ঐন্দ্রজালিক এক্রিয়াব পর কার্য আরম্ভ করে। এখন আমাদের দেশের কারিগরেরা করেন বিশ্বকর্মা পূজা এবং রক্তের বদলে ব্যবহার করেন সিন্দুর।[৩৭]
.
# শুভাশুভ লগ্ন ও খনার বচন
যাত্রা বা কোন কার্যারম্ভে শুভাশুভ কাল নির্ণয়ের ঝোঁক এই দেশে কম নহে। স্বদেশে, বিদেশে, এমনকি কোনো উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঘরের বাহিরে যাইতে হইলেই শুভাশুভ কাল নির্ণয়ের চেষ্টা অনেকে করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে দেশীয় পঞ্জিকাগুলিই প্রধান শিক্ষক। তিথি, বার, নক্ষত্র এবং অমৃত, মাহেন্দ্র ও শূলযোগের দোষ-গুণ বিচার না করিয়া কোথায়ও যাত্রার বা কোনো কাজে হাত বাড়াইবার নিয়ম নাই। বিবাহ, দ্বিরাগমন, সাধভক্ষণ ও অন্নপ্রাশন হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষা দীক্ষা, হল প্রবাহ ও বীজবপনাদি কোনো কাজেই পঞ্জিকার লিখিত তারিখ ও সময় ভিন্ন এক মিনিট এদিক ওদিক করা একেবারেই নিষেধ। সুখের বিষয় এই যে, রেল, স্টিমার, কোর্ট-কাঁচারি বা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে এখন আর ঐ বিষয়ে আমল দেওয়া হয় না।
“দিকশূল” কথাটি নাকি খুব ভয়ানক। শুক্র এবং রবিবারে পশ্চিমে দিকশুল। ঐরূপ মঙ্গল ও বুধবারে উত্তরে, শনি ও সোমবারে পূর্বে এবং বৃহস্পতিবারে দক্ষিণে দিকশূল। দিকশূলে যাত্রা করিলে যাত্রীর নাকি মৃত্যুর সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু ঐসব মানিয়া চলিলে ব্যবসা-বাণিজ্য অচল হওয়ার সম্ভাবনা আরও বেশি।
বার বা মাস মাহাত্মের প্রচারণাও এই দেশে কম নহে। ভিন্ন ভিন্ন বার বা মাসের গুণাগুণ নাকি ভিন্ন ভিন্ন। কোনো কোনো বার বা মাস নাকি অতি উৎকৃষ্ট, আবার কোনো কোনো বার বা মাস নাকি অতি নিকৃষ্ট (শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা বা ফসল উৎপাদনের জন্য নহে)। কেহ কেহ বলেন, জন্মমাস বা জন্মবার-এ বিবাহ নিষিদ্ধ। কেহ কেহ এই কথাও বলিয়া থাকেন যে, ভালো বার বা ভালো মাসে জন্সিতে বা মরিতে পারিলেও ভালো ফল পাওয়া যায়।
এইদেশে খনার বচন’ বলিয়া কতক শ্লোক প্রচলিত আছে এবং উহার অনেকগুলিতে আছে শুভাশুভ কাল নির্ণয়ের নির্দেশ। এইখানে উহার একটি নমুনা দেওয়া গেল।
“শূন্য কলসি, শুকনা না’, শুকনা ডালে ডাকে কা’,
যদি দেখ মাকুন্দ চোপা, এক পা না বাড়াও বাপা,
খনা বলে একেও ঠেলি, যদি সামনে না দেখি তেলি।”
অর্থাৎ জলহীন কলসি, আরোহী বা মালহীন নৌকা, মাকুন্দ অর্থাৎ দাড়ি-গোফ গজায় না এরূপ ব্যক্তি (মতান্তরে ধোপা) দৃষ্টিপথে পতিত হইলে এক পদও অগ্রসর হওয়া নিষেধ। যদি কোনো কারণে ইহার অন্যথা করাও হয়, তথাপি কলুর মুখ দেখিলে নিশ্চয়ই সেই যাত্রা ত্যাগ করিবে। বর্তমানে অয়েল মিলের মালিকেরাও কলু নামের আওতায় পড়ে, কিন্তু তাহাদের নিয়া যাত্রাভঙ্গের প্রশ্ন উঠে না।
খনার মতে, হাঁচি ও টিকটিকির শব্দ হইলে উহা কোন্ দিকে হইল এবং সাপ, শিয়াল, নেউল (বেজি) ইত্যাদি পথ ডিগাইলে, উহা কোন পার্শ্ব হইতে কোন পার্শ্বে গেল, তাহাও যাত্রার শুভাশুভ নির্দেশ করে। ডান বা বাম নাকে শ্বাস-নিঃশ্বাস চলাচলের তারতম্যও নাকি যাত্রাকালীন শুভাশুভ নির্দেশক।
.
# ভাগ্য
ফলিত জ্যোতিষ (Astrology)-এর সিদ্ধান্তমতে, প্রতিটি মানুষ জন্মিবার কালেই নক্ষত্রাদির সমাবেশে এক একটি রাশি প্রাপ্ত হয়। ইহাকে বলা হয় জন্মরাশি। মেষ, বৃষ, মিথুনাদি রাশির সংখ্যা বারোটি। মানুষ জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত যে রোগ, শোক, দুঃখ, পুত্র, কন্যা, বিত্ত-সম্পদ ও মান-অপমান ইত্যাদির অধিকারী হইয়া থাকে ইহার নিয়ামক তাহার রাশি। আবার কেহ কেহ বলেন যে, উহা রাশি নহে, ভাগ্য।
কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের যাবতীয় ঘটনাই নির্ধারিত হয় তাহার জন্মিবার বহু আগে ও তাহা লেখা থাকে তাহার ভাগ্যলিপিতে। বাঁচা, মরা, খাওয়া-দাওয়া এবং আয়-ব্যয়ের উপর মানুষের কোনো হাত নাই, উহা সমস্তই ভাগ্যলিপির ফল।
সুখের বিষয় এই যে, আজকাল প্রায় সকল মানুষই অদৃষ্টবাদ বনাম কুঁড়েমিবাদ পরিত্যাগ করিয়া কর্মবাদ গ্রহণ করিতেছেন এবং পৃথিবী হইয়া উঠিতেছে কর্মমুখর।
.
# সতীদাহ
প্রাচীন ভারতের একটি বিশেষ প্রথা অধুনালুপ্ত সতীদাহ। রমণী মরণান্তে অনন্তকাল স্বামীসহ স্বর্গবাস করিবে– এই বিশ্বাসের ফলেই সতীদাহ প্রথার প্রচলন হইয়াছিল।
সতীদাহ দুই রকম –সহমরণ ও অনুমরণ। পতির দেহের সহিত একত্রে দগ্ধ হওয়া সহমরণ এবং দূরদেশস্থ পতির মৃত্যু হইলে দেহের অভাবে পতির ব্যবহার্য কোনো দ্রব্য লইয়া চিতানলে দগ্ধ হওয়া অনুমরণ। গর্ভবতী রমণীর সহমরণে যাইবার অধিকার ছিল না। কিন্তু সন্তান প্রসবের পর অনুমরণের বিধান ছিল। পতির মৃত্যুর পর সহমরণাভিলাষিনী রমণী একটি আম্রপল্লব হস্তে ধারণ করিত। নববিধবা আম্রপল্লব ধারণ করিলেই ‘সহমরণে কৃতসংকল্পা’ বলিয়া লোকে বুঝিতে পারিত। মৃত ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকিলে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইত। কেননা একাধিক রমণীর সহমরণে অধিকার ছিল না। শাস্ত্রজ্ঞ গুরু-পুরোহিত বা আত্মীয়-স্বজনগণ গোলযোগ নিষ্পত্তি করিয়া একজনকেই নির্বাচন করিতেন। সহমরণোদ্ধতা রমণী রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া এবং সিন্দুর ও অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া পতির শবের অনুগমন করিত। অগ্রে শবদেহ বাহিত হইত। সতী শবের পশ্চাতে চলিত এবং তাহার পশ্চাতে আত্মীয়বর্গ ও কতিপয় ব্যক্তি ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গাদি বাদ্য করিতে করিতে হরিধ্বনি করিয়া শ্মশানে উপস্থিত হইত। তথায় দুই হাত প্রশস্ত, তিন হাত দীর্ঘ এবং তিন হাত উচ্চ চিতা সজ্জিত হইত। সতী পতিকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া চিতার উপর শয়ন করিত। তখন চিতায় অগ্নিসংযোগ করা হইত। সতী সহাস্যবদনে প্রজ্জ্বলিত চিতামধ্যে থাকিয়া পতিসহ ভস্মীভূত হইত। কোনো রমণী যদি চিতা দেখিয়া ভয়। পাইত, তবে তাহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনা হইত। কিন্তু চিতায় আরোহণ করিয়া ভয় পাইলে বা : প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাহাকে বলপূর্বক দাহ করা হইত।
এই বিষয়ে ‘পদ্মপুরাণ’-এ একটি উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। উপাখ্যানটি এইরূপ –
দেবরাজ ইন্দ্র একদা শিবলোকে এক ভয়কর পুরুষকে দেখিয়া তাহার পরিচয় জানিতে চাহিলে, সে তাহার কোনো উত্তর না দেওয়ায় ইন্দ্র কুদ্ধ হইয়া তাহাকে বজু দ্বারা আঘাত করেন। ইহাতে আগন্তুক পুরুষের ললাট হইতে অগ্নি নির্গত হইয়া ইন্দ্রকে জ্বালাইতে থাকে। তখন। আগন্তুক পুরুষকে রুদ্র বলিয়া চিনিতে পারিয়া ইন্দ্র তাহার স্তব-স্তুতি আরম্ভ করেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া রুদ্র তাহার ললাটের অগ্নি সাগর সঙ্গমে নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ উহা হইতে এক বালক উৎপন্ন হইয়া রোদন করিতে থাকে। সাগর ঐ বালকের জাতকর্মাদি নির্বাহের জন্য ব্রহ্মাকে অনুরোধ করে। ব্রহ্মা বালককে ক্রোড়ে লইবামাত্র সে তাহার দাড়ি ধরিয়া টান দিলে ব্রহ্মার চক্ষু হইতে জলধারা নির্গত হওয়ায় ঐ শিশুর নাম রাখিলেন জলন্ধর। অধিকন্তু ঐ শিশুকে বর দান করিলেন যে, সে অসুররাজ্যের রাজা হইবে এবং শিব ভিন্ন অপর কাহারও হস্তে তাহার মৃত্যু হইবে না।
বয়স্ক হইয়া জলন্ধর কালনেমির কন্যা বৃন্দার পাণি গ্রহণ করে এবং অসুররাজ্যের রাজা হয়। ক্রমে অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইয়া দেবরাজ ইন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া স্বর্গরাজ্য দখল করে। ইহাতে দেবতারা শিবের শরণাপন্ন হইলে শিব জলন্ধরকে বধ করার জন্য তাহার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ঐদিকে জলন্ধরের সহধর্মিনী বৃন্দা স্বামীর জীবনরক্ষার্থে বিষ্ণুর স্তব করিতে থাকে এবং বিষ্ণুর অনুকম্পায় জলন্ধর শিবেরও অবধ্য হইয়া উঠে। এই ঘটনা জানিতে পারিয়া দেবতারা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। তখন বিষ্ণু জলন্ধরের রূপ ধারণ করিয়া বৃন্দার নিকট উপস্থিত হইলে বৃন্দা বিষ্ণুর স্তব ত্যাগ করিয়া স্বামীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে এবং সেই অবসরে শিব জলন্ধরকে বধ করেন।
বিষ্ণুর ছল-চাতুরি ও স্বামীর মৃত্যুসংবাদ অবগত হইয়া বৃন্দা হতাশ হৃদয়ে বিষ্ণুকে অভিশাপ দিতে উদ্যতা হইলে বিষ্ণু তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, “তুমি তোমার পতির অনুমৃতা হও, তোমার ভস্মে যে বৃক্ষ জন্মিবে, তাহা আমার স্বরূপ হইবে। ঐ বৃক্ষকে পূজা করিলে আমার তুষ্টি জন্মিবে।”
অতঃপর বৃন্দা বিষ্ণুর উপদেশমতো কার্য করিলে বৃন্দার ভস্ম হইতে তুলসী, ধানী (আমলকি), পলাশ ও অশ্বথ বৃক্ষ উৎপন্ন হইল। হিন্দুগণ এই বৃক্ষচতুষ্টয়কে আজিও দেবতাজ্ঞানে ভক্তি ও পূজা করিয়া থাকেন।
পদ্মপুরাণের লেখক এই কাল্পনিক উপাখ্যানটির মাধ্যমে বিষ্ণুর মুখ দিয়া বৃন্দাকে আer অনুমরণের যে প্রেরণা দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে উদ্বুদ্ধা হইয়া যে কত হিন্দু রমণী অকালে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে?
মোগল সম্রাট মহামতি আকবর ইহার নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ইহা একেবারে রহিত করিতে পারেন নাই। অবশেষে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ কতিপয় দেশীয় লোকের সহযোগিতায় ১৮২৯ অব্দের ৪ ডিসেম্বর এক আইন করিয়া এই প্রথা রহিত করিয়া দেন। উক্ত আইনের মর্ম এই যে, অতঃপর যে কেহ সতীদাহে সহায়তা করিবে, সে ‘অপরাধযুক্ত নরহত্যা’ অপরাধে অপরাধী হইয়া দণ্ডনীয় হইবে। তদবধি হিন্দুদের সতীদাহ প্রথা স্থগিত আছে।
সতীদাহ প্রথা রহিতকরণে বেন্টিক সাহেবের সপক্ষে ছিলেন মাত্র গুটিকয়েক হিন্দু, গোড়ারা ছিলেন বিপক্ষে এবং অধিকাংশই ছিলেন মনোক্ষুণ্ণ। তখন হিন্দু ভারত স্বাধীন থাকিলে ঐ প্রথাটি বোধ হয় আজও প্রচলিত থাকিত। ভারত এখন স্বাধীন দেশ, কে জানে ভারত সরকার উহা পুনঃ প্রবর্তন করিবেন কি না!
.
# ভবিষ্যত গণনা
মানুষের ভবিষ্যত জানিবার কৌতূহল খুবই পুরাতন ও ব্যাপক এবং উহার জন্য নানা দেশে নানাবিধ নিয়ম প্রচলিত আছে। ভবিষ্যত জানিবার জন্য কয়েকটি অদ্ভুত প্রথা ছিল প্রাচীন ব্যাবিলোনিয়ায়। কোনো ব্যক্তির কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যের ভবিষ্যত শুভাশুভ জানিতে হইলে সে। একটি পশু বলিদান করিত এবং সেই পশুর যকৃতের উপরিস্থ রেখা বা দাগ দেখিয়া জানিয়া লওয়া হইত যে, বলিদাতার উদ্দেশ্যটির ভবিষ্যত শুভ কি অশুভ। ব্যাবিলোনিয়ার কোনো রাজাই নাকি উক্ত প্রথায় ফলাফল না জানিয়া যুদ্ধে যাইতেন না। এইরূপ প্রথা রোমানদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।
ঐ দেশে আর একটি প্রথা ছিল তৈল দ্বারা ভবিষ্যত জানা। কতগুলি পশু-পাখি বা পদার্থকে মনে করা হইত ভালো এবং কতগুলিকে মন্দ; আমরা যেমন ময়না, টিয়া পাখি ও জলপূর্ণ কলসি ভালো জানি, কিন্তু কাক, পেঁচক ও শূন্য কলসি ভালো জানি না। কোনো একটি জলপূর্ণ পাত্রে এক ফোঁটা তৈল ফেলিয়া লক্ষ্য করা হইত যে, উহা কি রকম আকৃতি ধারণ করে এবং সেই আকৃতি দেখিয়াই জানিয়া লওয়া হইত উদ্দেশ্যটির ভবিষ্যত শুভ কি অশুভ।[৩৮] এই ধরণের প্রথা কোনো কোনো অঞ্চলে প্রকারান্তরে এখনও প্রচলিত আছে।
এই দেশেও ভবিষ্যত জানার জন্য কয়েক রকম চেষ্টা প্রচলিত আছে। আগামী অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ, ধুমকেতুর উদয় ইত্যাদির বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে গণিত জ্যোতিষ (Astronomy) এবং যান্ত্রিক উপায়ে পাইয়া থাকি আবহাওয়ার পূর্বাভাস। আবার কেহ কেহ হাত বা কররেখা দেখিয়া কোনো ব্যক্তির জীবনের ভূত-ভবিষ্যত ও বর্তমানের সমস্ত ঘটনাই আগাম বলিয়া দেন। কাক, পেঁচক ও হুতুম পাখির ডাকও নাকি মানুষের ভবিষ্যত শুভাশুভের ইঙ্গিত করে এবং চক্ষুস্পন্দন, গাত্রচর্মের শিহরণও নাকি মানুষের ভবিষ্যত শুভাশুভের সংবাদ বহন করে।
এই দেশে প্রচলিত অনেক খনার বচন-এ ভবিষ্যত জানার উপায় বর্ণিত আছে। উহার একটি নমুনা–
(গর্ভস্থ সন্তান গণনা )
গ্রাম গর্ভিনী ফলে যুথা, তিন দিয়ে হর পুতা;
একে সুত, দুয়ে সুতা, শূন্য হলে গর্ভ মিথ্যা।
এ কথা যদি মিথ্যা হয়, সে ছেলে তার বাপের নয়।
অর্থাৎ যে গ্রামে গর্ভিনী বাস করে, সেই গ্রামের ও গর্ভিনীর নামের অক্ষরসংখ্যা এবং প্রশ্নকর্তা একটি ফলের নাম বলিবে, সেই ফলের নামের অক্ষরসংখ্যা একত্র করিয়া যোগফলকে তিন দ্বারা ভাগ করিতে হইবে। ভাগশেষ এক থাকিলে পুত্র, দুই থাকিলে কন্যা এবং শূন্য থাকিলে বুঝিবে যে, সেই গর্ভে সন্তান নাই। যদি কখনও এই গণনার ব্যতিক্রম হয়, তবে সেই সন্তানটি তাহার পিতার নহে, অর্থাৎ জারজ।
.
# ঠুকনো
প্রাচীনকালের ইহুদি পুরোহিতগণ তাহাদের শিষ্যদের এমন কতগুলি বিষয় শিক্ষা দিতেন, যাহা একান্তই তাহাদের অলীক কল্পনা। অথচ শিষ্যরা তাহা মনে প্রাণে বিশ্বাস ও প্রতিপালন করিত। পুরোহিতদের সেই সকল শিক্ষার কতগুলি বিষয় স্থান পাইয়াছে উহাদের তালমুদ গ্রন্থের ‘গেমারা’ অংশে। কালক্রমে উহা ভাষান্তরে (হয়তো বা রূপান্তরেও) বিস্তার লাভ করিয়াছে অন্যান্য জাতির মধ্যে। তালমুদীয় শিক্ষাগুলি এইরূপ —
১. বাড়িতে ভোজদ্রেব্য ঝুলাইয়া রাখিলে দারিদ্র দেখা দেয়।
২. বাড়িতে খুদ-কুঁড়া রাখিলে অভাব দেখা দেয়।
৩. বদনার মুখে ময়লা থাকিলে অভাব দেখা দেয়।
৪. প্লেট হইতে জল পান করিলে চক্ষে ছানি পড়ে।
৫. হাত না ধুইয়া রক্ত মোক্ষণ করিলে ৭ দিন বিভীষিকাদর্শন হয়।
৬. নাসারন্ধে হাত দিবার ফল বিভীষিকাদর্শন।
৭. কপালে হাত রাখিবার ফল নিদ্রা।
৮. খাদ্যদ্রব্য লৌহপাত্রে ঢাকা দিয়া রাখিলে উহা দানবের আশ্রয়স্থল হয়। ইত্যাদি।
এই দেশেও ঐ ধরণের কতগুলি প্রথা আছে, যাহা গ্রামাঞ্চলে বেশ প্রচলিত। যেমন—
১. লাউ, কুমড়া বা সীমের মাচায় কালো পাতিল রাখা। উহাতে নাকি লোকের কুদৃষ্টি এড়ানো যায় এবং গাছ সতেজ হয়।
২. শিশুর গলায় রুদ্রাক্ষ, ঝাটার শলা, তাবিজ-কবচ দেওয়া এবং কপালে তিলক কাটা। উহাতে নাকি ভূতপ্রেত বা দেও-দানবের আছর ও রোগের প্রকোপ এড়ানো যায়।
৩. মেয়েলোকের যমজ ফল না খাওয়া। খাইলে নাকি যমজ সন্তান হয়।
৪. সাধু-সজ্জন ও দেবতার নামে ছেলে-মেয়েদের নাম রাখা। ইহাতে নাকি দেশে চোর, বদমায়েশ ও অসৎ লোক কমিয়া থাকে।
৫. নানাবিধ রোগারোগ্য ও অভীষ্টসিদ্ধির জন্য মানত করা। ইত্যাদি।
————
৩৪. প্রাচীন মিশর, শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৪৬।
৩৫. প্রাচীন ইরাক, শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃ ১১৩-১১৫।
৩৬. প্রাচীন প্যালেস্টাইন, শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ২১৩-২১৮।
৩৭. প্রাচীন ইরাক, শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৮, ৯।
৩৮. প্রাচীন ইরাক, শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ১০৪।
১৫. কতিপয় ধর্মগ্রন্থ সৃষ্টি
কতিপয় ধর্মগ্রন্থ সৃষ্টি
সভ্য মানব সমাজে ধর্ম বহু এবং ধর্মগ্রন্থও অনেক। উহার মধ্যে কয়েকটিকে বলা হয় ঐশ্বরিক বা অপৌরুষেয় গ্রন্থ। এইখানে কয়েকখানা প্রসিদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হইল।
# ১. বেদ
হিন্দুদের মূল ধর্মগ্রন্থ বেদ। এই দেশের আর্য হিন্দুদের একান্ত বিশ্বাস যে, পরমপিতা ভগবান অগ্নি, বায়ু, আদিত্য ও অগিরা– এই চারিজন ঋষিকে সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধচিত্ত দেখিয়া ঘঁহাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া, এই চারিজনের মুখ দিয়া ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব এই চারি বেদ প্রকাশ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, বেদ সেই অনাদি অনন্ত ঈশ্বরের নিঃশ্বাসে সৃষ্ট, কোনো মানুষ ইহার রচয়িতা নহেন। বেদ অপৌরুষেয়।
হিন্দু ধর্মের যাবতীয় একান্ত করণীয় বিষয়ই বেদে বর্ণিত আছে। ঋকবেদ প্রধানত একখানি স্তোত্রগ্রন্থ। আর্য ঋষিগণ যে সকল মন্ত্র দ্বারা ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের আরাধনা করিতেন, সেই মন্ত্রগুলিই ঋকবেদের মূলসূত্র। ঐতিহাসিকদের মতে, বেদ ঐশ্বরিক পুঁথি নহে। কেননা ইহাতে প্রাচীন মুনি-ঋষিদের ও আর্য রাজাদের ইতিহাস পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, জনপদ, যুদ্ধবর্ণনা ইত্যাদি বেদে উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাদের মতে, ইহা আর্য সভ্যতার ইতিহাস মাত্র।
ঈশ্বর সর্বজ্ঞ। তাহার প্রণীত গ্রন্থে কখনও একদেশদর্শিতা দোষ থাকিতে পারে না। কিন্তু বেদে উহা আছে। বেদের যাবতীয় কারবা ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ। ভারতের বাহিরের বর্ণনা বিশেষ কিছু বেদে পাওয়া যায় না।
ঋগ্বেদে ২১৪ জন ঋষির নাম পাওয়া যায় এবং স্ত্রীলোকের নামও আছে ১২টি। বোধ হয় যে, উহারা সকলেই বেদের কোনো না কোনোও অংশের রচয়িতা। বস্তুত বেদে লিখিত শ্লোকগুলি তৎকালীন আর্য ঋষিদের ধ্যান-ধারণা, অভিজ্ঞতা ও কল্পনার সৃষ্টি।
বেদ যে ঋষিগণ কর্তৃক রচিত, তৎপ্রমাণ ঋগ্বেদেই রহিয়াছে। এইখানে আমরা ঋগ্বেদের কয়েকটি সূত্রের অনুবাদ লিপিবদ্ধ করিলাম। যথা —
১. হে অশ্বযোজক ভগবান! গৌতমাদি ঋষিরা তোমার উদ্দেশে এই মন্ত্র রচনা করিয়াছেন।
২. হে মরুত! এই নমস্কারজনক স্তোত্র অন্তরে রচিত হইয়া কায়মনে তোমাতে নিবেদিত হইল।
৩. আমাদিগের যজ্ঞবর্ধক বৈশ্যানর অগ্নির উদ্দেশে পবিত্র ঘৃততুল্য এক মন্ত্র রচনা করিয়াছি।
৪. সোমরস অভিযুত না হইলে ইন্দ্রের প্রীতি জন্মে না, আবার অভিযুত না হইলেও মন্ত্র ব্যতিরেকে তাহার প্রীতি জন্মে না, অতএব তাহার উদ্দেশে এক মনোহর স্তোত্র রচনা করিলাম।
৫. হে মিত্রাবরুণ! দীর্ঘত যজ্ঞশীল মহর্ষি বশিষ্ঠ তোমাদিগের উদ্দেশে এক সম্মানাহ স্তোত্র প্রেরণ করিতেছেন।
বেদ যে মনুষ্য (ঋষি) প্রণীত, তাহা উক্ত মন্ত্রগুলির অবস্থা দেখিলেই বুঝা যায়।
বেদের উৎপত্তিকাল সম্বন্ধে নানা মত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন খ্রী. পূ. ২,০০০ বৎসর, কেহ বলেন ৫,০০০ বৎসর। বাল গঙ্গাধর তিলক বেদমন্ত্র হইতেই বেদের বয়স গণনা করিয়াছেন ৮,০০০ বৎসর। পণ্ডিতবর উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিয়াছেন যে, বেদের বয়স অন্যূন ২১,৬০,০১৭ বৎসর। আবার কেহ বলেন, বেদ অনাদি। বেদের রচনাকাল সম্বন্ধে এতই। মতানৈক্য যে, কাহারও মতেই আস্থা স্থাপন করা যায় না। তবে এইকথা স্বীকার্য যে, বৈদিক স্তোত্রনিচয় এক সময়ে রচিত নহে, উহা সময়ে সময়ে ঋষিগণ দ্বারা এক এক অংশে রচিত হইয়াছিল। বর্তমান বেদ যাহা এখন জনসমাজে ব্যবহৃত ও পঠিত হইতেছে, ব্যাস-এর পূর্বে উহা এইরূপ ছিল না। অধুনাতন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বেদকে পৃথিবীর আদিগ্রন্থ বলিয়া নির্দেশ করেন।
বেদের রচনাকাল সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা থাকিলেও উহার সংকলন বা লিপিবদ্ধ করিবার কাল কিছু আন্দাজ করা চলে। হিন্দুদের মতে, কলি যুগ আরম্ভ হইয়াছে প্রায় ৫,০০০ বৎসর আগে। পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির রাজত্ব করিতেন দ্বাপর যুগের শেষ ও কলি যুগের শুরুতে এবং বেদগ্রন্থের সম্পাদক মহর্ষি ব্যাস ছিলেন তাঁহার পিতামহ। সুতরাং ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, গ্রন্থাকারে বেদের বয়স কিঞ্চিদধিক পাঁচ হাজার বৎসর।
মহর্ষি ব্যাস বেদের মন্ত্র সংকলন ও বিভাগ করেন বলিয়া তাহার আর এক নাম বেদব্যাস। হার রচিত মহাভারত ‘পঞ্চম বেদ’ নামে কথিত এবং অষ্টাদশ পুরাণ ইহারই রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই পুরাণাদি গ্রন্থসমূহও হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হয়। যদিও হিন্দু ধর্মকে বৈদিক ধর্ম বলা হইয়া থাকে, তথাপি বর্তমান হিন্দু ধর্ম হইল বৈদিক ও পৌরাণিক মতের সংমিশ্রণ। সে যাহা হউক, বৈদিক ও পৌরাণিক শিক্ষার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই —
১. ঈশ্বর এক (একমেবাদ্বিতীয়ম)।
২. বিশ্বজীবের আত্মাসমূহ এক সময়ের সৃষ্টি।
৩. মরণান্তে পরকাল এবং ইহকালের কর্মফল পরকালে ভোগ।
৪. পরলোকের বা পরজগতের দুইটি বিভাগ –স্বর্গ ও নরক।
৫. নরক অগ্নিময় এবং স্বর্গ উদ্যানময়।
৬. স্বর্গ সাত ভাগে এবং নরক সাত ভাগে বিভক্ত।
৭. স্বর্গ ঊর্ধদিকে এবং নরক নিম্নদিকে অবস্থিত।
৮. পুণ্যবানদের স্বর্গপ্রাপ্তি এবং পাপীদের নরকবাস।
৯. যমদূত কর্তৃক মানুষের জীবন হরণ।
১০. ভগবানের স্থায়ী আবাস ‘সিংহাসন’।
১১. স্তব-স্তুতিতে ভগবান সন্তুষ্ট। অর্থাৎ ভগবান তোষামোদপ্রিয়।
১২. মন্ত্র দ্বারা উপাসনা।
১৩. মানুষের আদিপিতা একজন মানুষ।
১৪. নরবলি হইতে পশুবলির প্রথা প্রবর্তন।
১৫. বলিদানে পুণ্যলাভ।
১৬. ঈশ্বরের নামে উপবাসে পুণ্যলাভ।
১৭. তীর্থভ্রমণে পাপের ক্ষয়।
১৮. ঈশ্বরের দূত আছে।
১৯. জানু পাতিয়া উপাসনায় বসা।
২০. সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত।
২১. করজোড়ে প্রার্থনা।
২২. মালা জপ।
২৩. নিত্য উপাসনার স্থান মন্দির।
২৪. নির্দিষ্ট সময়ে উপাসনা করা।
২৫. ধর্মগ্রন্থ পাঠে পুণ্যলাভ।
২৬. কার্যারম্ভে ঈশ্বরের নামোচ্চারণ। যথা –নারায়ণং নমস্কৃত্যং নবৈষ্ণব নরোত্তমম।
২৭. গুরুর নিকট দীক্ষা বা মন্ত্র গ্রহণ।
২৮. স্বর্গে গণিকা আছে। যথা– গন্ধর্ব, কিন্নরী, অপ্সরা ইত্যাদি।
২৯. উপাসনার পূর্বে অঙ্গ প্রক্ষালন।
৩০. দিগনির্ণয়পূর্বক উপাসনায় বসা। ইত্যাদি।
.
# ২. আমদুয়াত, ফটক ও মৃতের গ্রন্থ
প্রাচীন মিশরীয়দের ধর্মপুস্তক ছিল আমদুয়াত গ্রন্থ, ফটকের গ্রন্থ এবং মৃতের গ্রন্থ। প্রাচীন মিশরীয়রা ঐগুলিকে ঐশ্বরিক গ্রন্থ বলিয়া মনে করিত। কেননা উক্ত গ্রন্থত্রয়ের প্রত্যক্ষ কোনো রচয়িতা নাই এবং উহার আলোচ্য বিষয়সমূহের অধিকাংশই মানবজ্ঞানের বহির্ভূত। গ্রন্থত্রয়ের আলোচ্য বিষয়ের প্রায় সমস্তই পারলৌকিক জীবন বিষয়ক। মিশরীয়রা মনে করিত যে, পারলৌকিক জীবন বিষয়ক কোনো আলোচনা করা মানবীয় জ্ঞানে সম্ভব নহে। কেননা অতল ভবিষ্যতের খবর মানুষ জানিবে কি করিয়া? উহা হইবে অলৌকিক জ্ঞানসম্পন্ন কোনো অতিমানবের রচনা। সুতরাং গ্রন্থত্রয়ের রচয়িতা জ্ঞানের দেবতা থৎ এবং হাতের লেখাও তাহারই।
প্রাকপিরামিড যুগের মিশরবাসীগণ তাহাদের সমাধিমন্দিরগুলির গায়ে অথবা প্যাপিরাসে লিখিয়া বা অঙ্কিত করিয়া রাখিত মৃতের পরলোক বিষয়ক নানা রকম কম্পিত চিত্র। কালক্রমে ঐগুলির লেখক বা রচয়িতা কে কাহারা, তাহার কোনো হদিস পাওয়া যাইত না। পরবর্তী যুগের মানুষ মনে করিত যে, ঐ সমস্ত দৈব বা ঐশ্বরিক বাণী।[৩৯]।
আর্য ঋষিদের রচিত শ্লোকগুলিকে যেমন সংকলনপূর্বক উহা চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন মহর্ষি ব্যাস, প্রাচীন মিশরীয়দের সমাধিগাত্রে ও প্যাপিরাসে খচিত বিক্ষিপ্ত বাণীগুলিকেও তেমন সংকলনপূর্বক উহাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন সেকালের কোনো ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি।
পরলোক বা অধঃজগতের বিবরণ আছে বলিয়া প্রথম গ্রন্থটির নাম আমদুয়াত গ্রন্থ। দ্বিতীয়টির নাম ফটকের গ্রন্থ দেওয়া হইয়াছে এই জন্য যে, পরলোকে প্রত্যেকটি ঘণ্টার ব্যবধানে একটি করিয়া ফটক বা গেট আছে এবং মৃতকে সেই ফটকের ভিতর দিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে হয়। তৃতীয়টি, মৃতের গ্রন্থ, পরলোকবাসীদের জীবনবৃত্তান্ত। অর্থাৎ মরার পরের জীবন। গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে মৃতের গ্রন্থ খানাই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। উহাতে আছে পরজগতের বিস্তৃত বর্ণনা ও ইহজগতে থাকিয়া পরজগতের জীবনকে সুখী করিবার মন্ত্র ও ফরমুলা। উহার অধিকাংশই পিরামিড যুগের অর্থাৎ প্রায় খ্রী. পূ. ৩,০০০ অব্দের রচনা এবং কতক তাহারও আগের।
আলোচ্য গ্রন্থত্রয়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই –
১. স্বর্গদূত কর্তৃক সমাধিস্থ ব্যক্তির সত্যপাঠ গ্রহণ।
২. পাপ-পুণ্য পরিমাপের জন্য দাড়িপাল্লা ব্যবহার।
৩. মৃত ব্যক্তির পুনর্জীবন লাভ।
৪. পাপ-পুণ্যের বিচার।
৫. পরজগতের সুখের চাবিকাঠি ইহজগতেই। ইত্যাদি।
.
# ৩. জেন্দ-আভেস্তা
পারসিকদের ধর্মগ্রন্থ ‘জেন্দ-আভেস্তা’। পারসিকেরা উহাকে ঐশ্বরিক গ্রন্থ বলেন। তাঁহারা বলেন যে, তাঁহাদের ধর্মগুরু জোরওয়াস্টার একদা কোনো পর্বতশিখরে উপাসনায় আসীন থাকাকালে সেখানে বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎস্ফুরণের মধ্যে তাঁহার আরাধ্য দেবতা ‘অহুর মজদা’র আবির্ভাব হয় এবং তাহার নিকট হইতে তিনি জেন্দ-আভেস্তা গ্রন্থখানা প্রাপ্ত হন।
জোরওয়াস্টারের আবির্ভাব সম্বন্ধে নানা মত দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন যে, বিখ্যাত ট্রয় যুদ্ধের পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে জোরওয়াস্টার বিদ্যমান ছিলেন। ঐ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল খ্রী. পূ. ১১৯৩ সালে। এই হিসাবে জোরওয়াস্টারের আবির্ভাবকাল প্রায় খ্রী. পূ. ৬১৯৩ সাল। বেরোসাসের মতে জোরওয়াস্টারের আবির্ভাব খ্রী. পূ. ২৮০০ সালে। ডাইওনিসাস লেবার্টিয়াসের মতে জোরওয়াস্টারের আবির্ভাব খ্রী. পূ. ১৭৯৩ সালে এবং স্পিগেলের মতে খ্রী. পূ. ১৯২০ সালে। স্পিগেলের মত মানিয়া লইলে, জোরওয়াস্টার ও মহাপ্রবর ইব্রাহিম একই সময়ের মানুষ। কেননা হজরত ইব্রাহিম (আ.) খ্রী. পূ. ১৯২০ সাল বা তাহার কাছাকাছি সময়ে মিশর ভ্রমণে গিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।[৪০]
উপরোক্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায় যে, জোরওয়াস্টারের আবির্ভাব কমপক্ষে খ্রী. পূ. ১৭৯৩ সালে। সুতরাং জেন্দ-আভেস্তা গ্রন্থখানার বর্তমান বয়স প্রায় পৌনে চারি হাজার বৎসর।
জেন্দ-আভেস্তার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই —
১. উপাসনা পদ্ধতি –পারসিকগণের উপাসনার সময় একজন বিজ্ঞ ও ধার্মিক ব্যক্তি সম্মুখে দণ্ডায়মান হন, অন্যান্য সকলে তাহার পশ্চাতে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকেন। প্রথমে তাহারা যুক্তকরে দণ্ডায়মান থাকিয়া একবার মস্তক নত করেন, পরে ভূমিলগ্ন হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করেন ও পুনরায় সরলভাবে দণ্ডায়মান হন।
২. ঈশ্বরের নামোচ্চারণপূর্বক কার্যারম্ভ করা। কোনো কাজের শুরুতে পারসিকগণ বলিয়া থাকেন, “বানাম বাজদ বাকসিস গারদার”।
৩. অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদের সংমিশ্রণ। পারসিকগণ অদ্বৈতবাদ স্বীকার করেন এবং বলেন, “নেস্তেযাদ মগর যাজদান”–অর্থাৎ ঈশ্বর অদ্বিতীয়। আবার বলেন, সৎকাজের উদ্যোক্তা অহুর মজদা (পারসিকদের ঈশ্বর) এবং অসৎকাজের সৃষ্টিকর্তা আহরিমান। অর্থাৎ সৎকাজের প্রেরণাদাতা একজন এবং অসৎকাজের প্রেরণাদাতা আরেকজন। এমতাবস্থায় স্বভাবত ইহাই মনে হয় যে, হয়তো আহরিমানের কাজে বাধাদানের ক্ষমতা অহুর মজদার নাই, নতুবা তিনি ইচ্ছাপূর্বক বাধা দেন না। অর্থাৎ তিনি চক্রান্তকারী বা ভণ্ড।
৪. পরলোক সম্বন্ধে জেন্দ-আভেস্তার শিক্ষা —
ক. মৃত্যুর পর মানবদেহ দানবে অধিকার করে।
খ. মৃত্যুর পর দণ্ড ও পুরস্কার আছে।
গ. পরলোকে প্রত্যেক ব্যক্তিকে চিনাভাদ নামক পুল পার হইতে হয়। পুণ্যবানগণ অনায়াসে উহা পার হইতে পারে। কিন্তু পাপীগণ দুখ নামক দুঃখার্ণবে নিপতিত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে।
ঘ. উপাসনা ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যস্থতায় কাহারও কাহারও দুঃখভোগের কাল হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।
ঙ. এই যুগের শেষ ভাগে সওসন্ত নামক একজন মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইবেন।
চ. ছয় দিনে জগতসৃষ্টি এবং উহার শেষদিনে মানুষসৃষ্টি। আদি মানুষটির নাম গেওমাড। ইত্যাদি।
.
# ৪. বাইবেল
পবিত্র বাইবেল গ্রন্থ ৬৬খানা ক্ষুদ্র পুস্তকের সমষ্টি এবং উহা দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগকে বলা হয় পুরাতন নিয়ম (Old Testament), ইহাতে পুস্তকের সংখ্যা ৩৯ এবং দ্বিতীয় ভাগকে বলা হয় নূতন নিয়ম (New Testament), ইহাতে পুস্তকের সংখ্যা ২৭। মুসলমানগণ যাহাকে তাউরাত (তৌরিত) ও জব্দুর কেতাব বলেন, উহা পুরাতন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত এবং নূতন নিয়মের অন্তর্ভুক্ত ইঞ্জিল কেতাব। যাহারা পুরাতন নিয়ম মানিয়া চলেন, তাহাদিগকে বলা হয় ইহুদি এবং যাহারা নূতন নিয়ম অনুসরণ করিয়া চলেন, তাহাদিগকে বলা হয় খ্রীস্টিয়ান। উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই উক্ত গ্রন্থাবলীকে ঐশ্বরিক বলিয়া মনে করেন।
কিন্তু মুসলমানগণ তৌরিত, জব্বর ও ইঞ্জিল –এই নাম কয়টিকে ঐশ্বরিক বলিয়া স্বীকার করেন, গ্রন্থকে নহে। কেননা বলা হইয়া থাকে যে, হাল আমলে প্রচলিত গ্রন্থসমূহ আসল নহে, উহা কৃত্রিম। সে যাহা হউক, বাইবেলের অন্তর্গত তৌরিত, জব্বর ও ইঞ্জিল –এই গ্রন্থত্রয়ের পৃথক পৃথক আলোচনা করা যাইতেছে।
তৌরিত
ইহুদিদের মতে, একদা হজরত মূসা তুর পর্বতের চূড়ায় ভগবান জাভে (ইহুদিদের ঈশ্বর)-এর দর্শন লাভ করেন ও তাহার বাণী শ্রবণ করেন এবং জাভে-এর স্বহস্তে লিখিত দশটি আদেশ সম্বলিত দুইখানা পাথর প্রাপ্ত হন। উহাই তৌরিত গ্রন্থের মূলসূত্র। অতঃপর বহুদিন যাবত হজরত মূসা উক্ত পর্বতে যাতায়াত করিয়া ও অন্যত্র বিভিন্ন সময়ে জাভের নিকট হইতে যে সমস্ত আদেশ-উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাও উক্ত গ্রন্থে হান পাইয়াছে।
হজরত মূসার ঈশ্বরের দর্শনলাভ সম্বন্ধে তৌরিতের বিবরণটি এইরূপ — “মিশর দেশ হইতে ইস্রায়েল সন্তানদের বাহির হইবার পর তৃতীয় মাসে … পরে তৃতীয় দিন প্রভাত হইলে মেঘগর্জন ও বিদ্যুৎ এবং পর্বতের উপরে নিবিড় মেঘ হইল, আর অতিশয় উচ্চরবে তুরিধনি হইতে লাগিল; তাহাতে শিবিরস্থ সমস্ত লোক কাপিতে লাগিল … তখন সমস্ত সীনয় পর্বত ধূমময় ছিল। কেননা সদাপ্রভু অগ্নিসহ তাহার উপর নামিয়া আসিলেন, আর ভাটির ধূমের ন্যায় তাহা হইতে ধূম উঠিতে লাগিল এবং সমস্ত পর্বত অতিশয় কপিতে লাগিল। আর তুরির শব্দ ক্রমশ অতিশয় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন মোশি (মূসা আ.) কথা কহিলেন এবং ঈশ্বর বাণী দ্বারা তাঁহাকে উত্তর দিলেন।” (যাত্রাপুস্তক ১৯; ১, ১৬, ১৮, ১৯)
অন্যত্র হজরত মূসা বলেন, “সদাপ্রভু পর্বতের অগ্নির, মেঘের ও ঘোর অন্ধকারের মধ্য হইতে তোমাদের সমস্ত সমাজের নিকটে এই সমস্ত বাক্য মহারবে বলিয়াছিলেন, আর কিছুই বলেন নাই। পরে তিনি এই সমস্ত কথা দুইখানা প্রস্তরফলকে লিখিয়া আমাকে দিয়াছিলেন।” (দ্বিতীয় বিবরণ ৫; ২২)
উক্ত বিবরণে দেখা যায় যে, ঐদিন তূর পর্বত ধূম্রবৎ মেঘে আচ্ছন্ন ছিল এবং মুহুর্মুহু মেঘগর্জন হইতেছিল ও বিদ্যুৎচমকে পর্বতটি অগ্নিময় দেখাইতেছিল। প্রিয় পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে যে, পার্শি ধর্ম প্রবর্তক জোরওয়াস্টারও অনুরূপ বজ-বিদ্যুতের মধ্যে পাহাড়চূড়ায় তাঁহার ধর্মবিধি জেন্দ-আভেন্তা গ্রন্থখানা পাইয়াছিলেন।
ইস্রায়েল বংশীয় মহাভাববাদী হজরত মূসা মিশর দেশে জন্মগ্রহণ করেন খ্রী. পূ. ১৩৫১ সালে এবং তূর পর্বতে খোদাতা’লার নূর দেখিতে, বাণী শুনিতে ও দশ আদেশ খচিত প্রস্তরফলক পান খ্রী. পূ. ১২৮৫ সালে। অতঃপর ৫৪ বৎসরকাল স্বীয় ধর্মমত (ইহুদি ধর্ম) প্রচার করিয়া নিবো পাহাড়ে দেহত্যাগ করেন খ্রী. পূ. ১২৩১ সালে। কাজেই তৌরিত গ্রন্থের সৃষ্টি খ্রী. পূ. ১২৮৫ ১২৩১ সালের মধ্যে। সুতরাং তৌরিত গ্রন্থের বর্তমান বয়স অন্যূন ৩,২০০ বৎসর।
তৌরিত গ্রন্থের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এই —
১. ত্বকচ্ছেদ –অর্থাৎ পুরুষের লিঙ্গগ্রের চর্ম কর্তন করা। ইহা ইহুদিদের জাতীয় চিহ্ন। ইহা না করিলে সে ইহুদিদের স্বজাতীয় বলিয়া গণ্য হয় না। (লেবীয় ১২; ৩)
২. খাদ্য ও অখাদ্য নির্ণয় –খাদ্যাখাদ্য নির্ণয়ে তৌরিতের বিধান এইরূপ — “পশুগণের মধ্যে যে কোনো পশু সম্পূর্ণ দ্বিখণ্ড খুর বিশিষ্ট ও জাবর কাটে, তাহা তোমরা ভোজন করিতে পার। … আর শূকর তোমাদের পক্ষে অশুচি। কেননা সে সম্পূর্ণ দ্বিখণ্ড খুর বিশিষ্ট বটে, কিন্তু জাবর কাটে না। তোমরা তাহাদের মাংস ভোজন করিও না; এবং তাহাদের শবও স্পর্শ করিও না; তাহারা তোমাদের পক্ষে অশুচি।
“জলজন্তুদের মধ্যে তোমরা এই সকল ভোজন করিতে পার –জলাশয়ে, সমুদ্রে কি নদীতে স্থিত জন্তুর মধ্যে ডানা ও আঁইশ বিশিষ্ট জন্তু তোমাদের খাদ্য।… পক্ষীদের মধ্যে এই সকল তোমাদের পক্ষে ঘৃণাহ হইবে –ঈগল, হাড়গিলা, কুরল, চিল, … কাক, উষ্ট্রপক্ষী, রাত্রিশ্যেন, গাংচিল, শ্যেন, পানি ভেলা, পেঁচক, মাছরাঙ্গা, মহাপেঁচক, দীর্ঘগল হংস, শকুনী, সারস, বক, টিভি ও বাদুড়, … আর তোমাদের কোনো পশু মরিলে, যে কেহ তাহার শব স্পর্শ বা ভক্ষণ করিবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকিবে।” (লেবীয় পুস্তক ১১; ৩, ৬৯, ১৩–১৯, ৩৯)
৩. অশুচিতা –অশৌচ সম্বন্ধে তৌরিতের বিধান এইরূপ — “আর সদাপ্রভু মোশিকে কহিলেন, তুমি ইস্রায়েল সন্তানগণকে বল, যে স্ত্রী গর্ভধারণ করিয়া পুত্র প্রসব করে, সে সাতদিন অশুচি থাকিবে, … পরে অষ্টম দিনে বালকটির ত্বকচ্ছেদ হইবে [ত্বকচ্ছেদ নিয়মটির প্রবর্তক হজরত ইব্রাহিম (আদিপুস্তক ১৭; ১০-১২) ]। আর সে স্ত্রী তেত্রিশ দিন পর্যন্ত আপনার শৌচার্থ রক্তস্রাব অবস্থায় থাকিবে। যাবত শৌচাৰ্থ দিন পূর্ণ না হয়, তাবৎ সে কোনো পবিত্র বস্তু স্পর্শ করিবে না এবং ধর্মধামে প্রবেশ করিবে না।… আর যে স্ত্রী রজস্বলা হয়, তাহার শরীরস্থ রক্তক্ষরণে সাত দিবস তাহার অশৌচ থাকিবে। আর অশৌচকালে সে যে কোনো শয্যায় শয়ন করিবে, তাহা অশুচি হইবে ও যাহার উপর বসিবে, তাহা অশুচি হইবে।” (লেবীয় পুস্তক ১২; ১৪ ও ১৯; ১৯-২০)
৪. রেতস্থলন –“আর যদি কোনো পুরুষের রেতপাত হয়, তবে সে আপনার সমস্ত শরীর জলে ধৌত করিবে।… আর যে কোনো বস্ত্রে কি চর্মে রেতপাত হয়, তাহা জলে ধৌত করিতে হইবে।… আর স্ত্রীর সহিত পুরুষ রেতশুদ্ধ শয়ন করিলে, তাহারা উভয়ে জলে স্নান করিবে। (লেবীয় ১৫; ১৬-১৮)
৫. বিবাহ নিষিদ্ধ নারী –তৌরিত গ্রন্থে নিম্নলিখিত আত্মীয়া রমণীগণের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। মাতা, বিমাতা, ভগিনী, নাতিনী, বৈমাত্র ভগিনী, পিসী, মাসী, চাচী, পুত্রবধূ, ভ্রাতৃবধূ, স্ত্রীর নাতিনী (পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত), স্ত্রীর কন্যা (পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত), শাশুড়ী। (লেবীয় ১৮; ৬-১৭)
৬. অশৌচকালে যৌনমিলন নিষিদ্ধ –“কোনো স্ত্রীর অশৌচকালে তাহার আবরণীয় অনাবৃত করিতে তাহার নিকটে যাইও না।” (লেবীয় পুস্তক ১৮; ১৯)
৭. ঈশ্বর নামের নিন্দায় জীবনদণ্ড –“আর যে সদাপ্রভুর নামের নিন্দা করে, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে। সমস্ত মণ্ডলী তাহাকে প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে, বিদেশীয় হউক আর স্বদেশীয় হউক, সেই নামের নিন্দা করিলে উহার প্রাণদণ্ড হইবে।” (লেবীয় পুস্তক ২৪; ১৬)
অহিংসা পরম ধর্ম –এই বাক্যটিতে সকল ধর্মই একমত। অথচ ধর্মে-ধর্মে হিংসার অন্ত নাই, বিশেষত ঈশ্বর সম্বন্ধে। নিরীশ্বরবাদী (নাস্তিক) মানুষের সংখ্যা জগতে খুবই অল্প এবং প্রায় সকল ধর্মই ঈশ্বরবাদী এবং ঈশ্বরের সংজ্ঞাও প্রায় একই, তখন সমস্ত জগতে সর্বসম্মত একজন ঈশ্বর থাকা উচিত। কিন্তু আছে কি?
নামে পরিবর্তনে বিশেষ কিছু আসে যায় না। বিভিন্ন ভাষায় সূর্যের নাম বিভিন্ন। কিন্তু উহার আকৃতি ও প্রকৃতি সর্বত্রই একরূপ। কিন্তু পরমেশ্বর, অহুর মজদা, জাভে, পরমপিতা ও আল্লাহ প্রভৃতি ঈশ্বরবাচক নামগুলি যেমন ভিন্ন ভিন্ন, তেমন তাহার স্বভাব-চরিত্রও ধর্মজগতে ভিন্ন ভিন্ন। আবার প্রত্যেক ধর্মই অপর ধর্মাবলম্বী মানুষকে বলে বিধর্মী। ধর্ম বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা যেন তাহার নিজেরটিই; অন্য আর একটিও ধর্ম নহে, ঐসব কুসংস্কার।
প্রত্যেক ধার্মিকের কাছেই আপন ঈশ্বর প্রেমের পাত্র এবং ভক্তরা তাহার প্রশংসায় মুখর। কিন্তু অন্যদের ঈশ্বর যেমন প্রশংসার অযোগ্য, তেমন ঘৃণার পাত্র। এমতাবস্থায় বিধর্মী মাত্রেই ঈশ্বরনিন্দুক এবং তৌরিতের মতে তাহারা বধের যোগ্য। কাজেই ইহাতে সৃষ্ট হইল বিজাতিবিদ্বেষ ও তাহার পরিণামে ধর্মযুদ্ধ। কে বলিতে পারে যে, কত মানুষ প্রাণ দিয়াছে পুরোহিততন্ত্রের আমলের ধর্মযুদ্ধে? সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, গণতন্ত্রের যুগে ধর্মযুদ্ধ হইয়াছে অচল বা বাতিল। কিন্তু নির্বাণোন্মুখ প্রদীপের মতো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা এখনও ঘটিয়া থাকে।
৮. খুনের বদলে খুন –এই বিষয়ে তৌরিতের শিক্ষা এইরূপ — “আর যে কেহ কোনো মানুষকে বধ করে, তাহার প্রাণদণ্ড অবশ্য হইবে।” (লেবীয় পুস্তক ২৪; ১৭)
ইহুদি জাতির উক্ত নীতিটি আন্তর্জাতিক মর্যাদা লাভ করিয়াছিল — শূলদণ্ড ও ফাঁসিকাষ্ঠে। তবে বর্তমানে উহা অনেকেই পছন্দ করেন না।
৯. সুদের নীতি –“তোমার ভ্রাতা যদি দরিদ্র হয়, তবে তুমি তাহার উপকার করিবে … তুমি তাহা হইতে সুদ কিম্বা বৃদ্ধি লইবে না।” (লেবীয় পুস্তক ২৫; ৩৫, ৩৬)
১০. মানত করা –“যদি কেহ বিশেষ মানত করে, তবে তোমার নিরূপণীয় মূল্যানুসারে প্রাণীসকল সদাপ্রভুর হইবে।” (লেবীয় পুস্তক ২৭; ২)
মানত প্রথাটি এদেশের এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে এখনও বেশ প্রচলিত আছে। ছাগল-গরু হইতে আরম্ভ করিয়া মৎস্য, ফল-ফলাদি, এমনকি লাউ-কুমড়াদি, তরিতরকারিও মানত হইয়া মন্দির ও দরগাহে যাইয়া থাকে।
১১. উৎসর্গ –“আর যদি কেহ সদাপ্রভুর কাছে উৎসর্গের জন্য পশু দান করে, তবে সদাপ্রভুর উদ্দেশে দত্ত তাদৃশ সমস্ত পশু পবিত্র বস্তু হইবে।” (লেবীয় ২৭; ৯)
এতদ্দেশেও সদাপ্রভুর নামে পশু, বিশেষত গরু উৎসর্গের নিয়ম প্রচলিত আছে।
১২. দায়ভাগ বা উত্তরাধিকার –এই বিষয়ে তৌরিতের বিধান এইরূপ — “তুমি উহাদের পিতৃকুলের ভ্রাতাদিগের মধ্যে উহাদিগকে স্বত্বাধিকার দিবে ও উহাদের পিতার অধিকার উহাদিগকে সমৰ্পণ করিবে। …. কেহ যদি অপুত্রক হইয়া মরে, তবে তোমরা তাহার অধিকার তাহার কন্যাকে দিবে। যদি কন্যা না থাকে, তবে তাহার ভ্রাতৃগণকে তাহার অধিকার দিবে। যদি তাহার ভ্রাতা না থাকে, তবে তাহার পিতৃব্যদিগকে তাহার অধিকার দিবে। যদি তাহার পিতৃব্য না থাকে, তবে তাহার গোষ্ঠীর মধ্যে নিকটস্থ জ্ঞাতিকে তাহার অধিকার দিবে।” (গণনা পুস্তক ২৭; ৭-১১)
১৩. বিজাতিবিদ্বেষ –“আর তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যখন তোমার সম্মুখে তাহাদিগকে (বিজাতীয়দিগকে) সমর্পণ (পরাজিত) করিবেন, এবং তুমি তাহাদিগকে আঘাত করিবে, তখন তাহাদিগকে নিঃশেষে বিনষ্ট করিবে, তাহাদের সহিত কোনো নিয়ম (সন্ধি) করিবে না বা তাহাদের প্রতি দয়া করিবে না।” (দ্বিতীয় বিবরণ ৭; ২)
১৪. বলিদানে পশু নির্বাচন –“তুমি আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে দোষযুক্ত, কোনো প্রকার কলকযুক্ত গরু কিম্বা মেষ বলিদান করিবে না। কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তাহা ঘৃণা করেন।” (দ্বিতীয় বিবরণ ১৭; ১)
১৫. ব্যভিচারের ফল –“যদি কেহ পুরুষের প্রতি বাগদত্তা (বিবাহিতা) কোনো কুমারীকে নগরমধ্যে পাইয়া তাহার সহিত শয়ন করে, তবে তোমরা সেই দুইজনকে বাহির করিয়া নগরদ্বারের নিকটে আনিয়া প্রস্তরাঘাতে বধ করিবে … যদি কেহ অবাগদত্তা কুমারী কন্যাকে পাইয়া তাহাকে ধরিয়া তাহার সহিত শয়ন করে ও তাহারা ধরা পড়ে, তবে তাহার সহিত শয়নকারী সেই কন্যার পিতাকে পঞ্চাশ রৌপ্য (শেকেল) দিবে এবং তাহাকে মানভ্রষ্টা করিয়াছে। বলিয়া সে তাহার স্ত্রী হইবে; সেই পুরুষ তাহাকে যাবজ্জীবন ত্যাগ করিতে পারিবে না। (দ্বিতীয় বিবরণ ২২; ২৩, ২৪, ২৮, ২৯)
১৬. স্ত্রীত্যাগ –“কোনো পুরুষ কোনো স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়া বিবাহ করিবার পর যদি তাহাতে কোনো প্রকার অনুপযুক্ত ব্যবহার দেখিতে পায়, আর সেই জন্য সে স্ত্রী তাহার দৃষ্টিতে প্রীতিপাত্রী না হয়, তবে সেই পুরুষ তাহার জন্য এক ত্যাগপত্র লিখিয়া তাহার হস্তে দিয়া আপন বাটী হইতে তাহাকে বিদায় করিতে পারিবে।” (দ্বিতীয় বিবরণ ২৪; ১)
১৭. দশ আদেশ — তৌরিত গ্রন্থ বা ইহুদি জাতির প্রাণকেন্দ্র, ঈশ্বরের স্বহস্তে দুইখানা প্রস্তরে লিখিত বিখ্যাত দশ আদেশ এই—
আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য খোদা না থাকুক।
তুমি খোদিত প্রতিমা বানাইও না।
তুমি অনর্থক ঈশ্বরের নাম লইও না।
বিশ্রামদিন পালন করিও।
মাতাপিতাকে সমাদর করিও।
নরহত্যা করিও না।
ব্যভিচার করিও না।
চুরি করিও না।
প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।
প্রতিবেশীর গৃহে লোভ করিও না। (যাত্রাপুস্তক ২০; ৩-১৭)
বিখ্যাত দশ আদেশ ভুক্ত তৃতীয় আদেশটি কোনো কোনো মহলের বিস্ময় উৎপাদন করে বটে, কিন্তু অধুনা ঐ আদেশটি ব্যাপকভাবেই প্রতিপালিত হইতেছে।
জব্বুর
কথিত হয় যে, হজরত দাউদ নবীর উপর জব্বুর কেতাব অবতীর্ণ হইয়াছিল। অর্থাৎ হজরত দাউদের আদেশ-উপদেশগুলিই জব্দুর কেতাব নামে অভিহিত। হজরত দাউদের জন্ম খ্রী. পূ. ১০৩১ সালে এবং মৃত্যু খ্রী. পূ. ৯৭১ সালে। সুতরাং হজরত দাউদের মৃত্যু হইয়াছে এখন (১৯৭০) হইতে ২,৯৪১ বৎসর পূর্বে। কাজেই জব্বুর গ্রন্থের সৃষ্টিকাল প্রায় উহাই।
লক্ষাধিক নবী-আম্বিয়াগণ সকলেই কিছু না কিছু ঐশ্বরিক বাণী প্রাপ্তির দাবি করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অনেকের বাণীই প্রাচীন বিধান বাইবেলে স্থান লাভ করিয়াছে। কিন্তু যীশু খ্রীস্টের পূর্ববর্তী কোনো নবীই হজরত মূসার ধর্মবিধি ব্যতীত অন্য কোনো ধর্মমত প্রচার করেন নাই। বরং প্রায় সকলেই ছিলেন হজরত মূসার মতের সমর্থক ও পরিপূরক। এমনকি হজরত দাউদও স্বতন্ত্র কোনো ধর্মমত প্রচার করেন নাই। বরং তিনি মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে স্বীয় পুত্র সোলায়মানকে বলিয়াছিলেন, “আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুর রক্ষণীয় বিধান রক্ষা করিয়া তাহার পথে চল, মোশির (হজরত মূসার) ব্যবস্থায় লিখিত তাহার বিধান, তাহার আজ্ঞা, তাহার শাসন ও তাহার সাক্ষ্যসকল পালন কর। (১ রাজাবলি ২; ৩)
ইঞ্জিল
ইঞ্জিলকে ঐশ্বরিক গ্রন্থ বলা হয়। কিন্তু ইহা তৌরিতের মতো মহাপ্রভুর নিজের মুখের বাণী নহে, যীশুর মুখের বাণী। যীশু কুমারী মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, লোকাঁচারে তাহার কোনো পিতা ছিল না। তাই বলা হয় যে, তিনি ঈশ্বরের পুত্র। আর পিতার পক্ষ হইতে কথা বলিবার অধিকার পুত্রের থাকে। সেই মর্মে যীশুর আদেশ-উপদেশ ও বিধি-নিষেধসমূহকে ঈসায়ীগণ ঐশ্বরিক বাণী রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন।
হজরত মূসা নবীর মতো যীশু (হজরত ঈসা আ.)-ও মহাপ্রভুর দর্শন পাইয়াছিলেন। যীশুর খোদাদর্শন সম্বন্ধে বাইবেলে লিখিত বিবরণটি এইরূপ — “পরে যীশু বাপ্তাইজিত হইয়া অমনি জল হইতে উঠিলেন, আর দেখ, তাহার নিমিত্ত স্বর্গ (আকাশ) খুলিয়া গেল; এবং তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায় নামিয়া আপনার উপরে আসিতে দেখিলেন, আর দেখ, স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল, ‘ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, হঁহাতেই আমি প্রীত।” (মথি ৩; ১৬, ১৭)
এতদ্দেশের হিন্দুগণ গঙ্গানদীর জলকে পবিত্র মনে করেন এবং মুসলমানগণ পবিত্র মনে করেন জমজম কূপের পানি। ঐরূপ ইহুদিরা (খ্রীস্টানরাও) জর্দান নদীর পানিকে পবিত্র মনে। করেন। ইহুদিদের স্বধর্মে দীক্ষা গ্রহণের সময় ঐ নদীর জলে অবগাহন করিতে হয়। উহাকে বলা হয় বাপ্তাইজ। যে সমস্ত দূরদেশবাসীদের পক্ষে ঐ নদীর জলে অবগাহন সম্ভব নহে, সেই সমস্ত দেশবাসীদের বাপ্তাইজিত হইতে হয় ঐ নদী হইতে লওয়া কিছু জল গায়ে ছিটাইয়া।
তৎকালীন ইহুদিদের ধর্মযাজক ছিলেন হজরত জাকারিয়া নবীর পুত্র হজরত ইয়াহইয়া (যোহন)। ত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে যীশু যোহনের নিকট ইহুদি ধর্মে বাপ্তাইজিত হন। অর্থাৎ দীক্ষা গ্রহণ করেন।
যীশু বাপ্তাইজিত হইয়া জর্দান নদীর তীরে উঠিয়া দেখিতে পাইলেন যে, একটি কবুতর পাখি উড়িয়া তাহার মাথার উপর আসিতেছে। তখন তিনি ভাবিলেন যে, ঐ কবুতরটি ঈশ্বরের আত্মা। আর তিনি শুনিতে পাইলেন, কবুতরটি বলিয়া গেল, “ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতেই আমি প্রীত।” এই বাণীটির দ্বারাই যীশু পাইলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধিত্ব।
যীশু ঈশ্বরের বাণী বা পয়গম্বরী প্রাপ্ত হন ৩০ বৎসর বয়সে। অতঃপর তিনি স্বীয় ধর্মমত (খ্রীস্টিয়ানিটি) প্রচার করিতে শুরু করেন। ধর্ম বিষয়ে তাঁহার মতামতসমূহই নূতন নিয়ম বা ইঞ্জিল কেতাব নামে পরিচিত। কাজেই ইঞ্জিল কেতাবের বর্তমান (১৯৭০) বয়স অনধিক ১৯৪০ বৎসর।
নূতন নিয়ম-এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিধান এই —
১. হিংসা করা নিষেধ –হজরত মূসা (আ.) বলিতেন যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চক্ষুর বদলে চক্ষু ও দন্তের পরিবর্তে দন্ত লইবে। কিন্তু যীশু বলিতেন, “তুমি দুষ্টের প্রতিরোধ করিও না। বরং যে কেহ তোমার ডান গালে চড় মারে, অন্য গাল তাহাকে ফিরাইয়া দাও। আর যে তোমার সহিত বিচারস্থানে বিবাদ করিয়া তোমার আঙরাখা লইতে চায়, তাহাকে চোগাও লইতে দাও। আর যে কেহ এক ক্রোশ যাইতে তোমাকে পীড়াপীড়ি করে, তাহার সহিত দুই ক্রোশ যাও।” (মথি ৫; ৩৯-৪১)
২. শপথ করা নিষেধ –হজরত মূসা (আ.) বলিতেন, “তুমি মিথ্যা দিব্য করিও না।” কিন্তু যীশু বলিতেন, “কোনো দিব্যই করিও না।” (মথি ৫; ৩৪)
৩. গোপনে দান করা –যীশু বলিতেন, “তুমি যখন দান কর, তখন তোমার দক্ষিণ হস্ত কি করিতেছে, তাহা তোমার বাম হস্তকে জানিতে দিও না।” (মথি ৬; ৩, ৪)
৪. সঞ্চয় না করা –যীশু বলিয়াছেন, “তোমরা পৃথিবীতে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয় করিও না; এইখানে তো কীটে-মরিচায় ক্ষয় করে এবং চোরে সিধ কাটিয়া চুরি করে। কিন্তু স্বর্গে আপনাদের জন্য ধন সঞ্চয় কর, সেইখানে কীটে ও মরিচায় ক্ষয় করে না, সেইখানে চোরেও সিধ কাটিয়া চুরি করে না।” (মথি ৬; ১৯, ২০)
যীশুর এই আদেশটি হাল জামানার অর্থনীতির পরিপন্থী। কেননা বর্তমান যুগের রাজনীতিতে অর্থনীতির ক্ষেত্রে সঞ্চয়কেই প্রথম স্থান দেওয়া হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে যীশুর এই আদেশটি ধর্মান্তরে প্রতিফলিত হওয়ার ফলে নিরীহ ধর্মভীরুদের শ্রমার্জিত অর্থ লুটিতেছে একদল ব্যবসায়ী ধর্মপ্রচারক।
৫. পরনিন্দা না করা –যীশু বলিয়াছেন, “তোমরা বিচার করিও না, যেন বিচারিত না হও। … আর তোমার ভ্রাতার চক্ষে যে কুটা আছে, তাহাই কেন দেখিতেছ, কিন্তু তোমার নিজের চক্ষে কড়িকাঠ আছে, তাহা কেন ভাবিয়া দেখিতেছ না?” (মথি ৭; ১-৩)
৬. সর্বস্ব ত্যাগ করা –একদা এক ব্যক্তি যীশুকে জিজ্ঞাসা করিল, “হে গুরু! অনন্ত জীবন পাইবার জন্য কিরূপ সৎকর্ম করিব?” যীশু বলিলেন, “নরহত্যা করিও না, চুরি করিও না, ব্যভিচার করিও না এবং তোমার প্রতিবেশীকে আপনার মতো প্রেম করিও।” সেই ব্যক্তি বলিল যে, “আমি ঐ সমস্ত আদেশ পালন করিয়াছি, এখন আমার কি ত্রুটি আছে?” উত্তরে যীশু তাহাকে বলিলেন, “যদি সিদ্ধ হইতে ইচ্ছা কর, তবে চলিয়া যাও, তোমার যাহা আছে, বিক্রয় কর এবং দরিদ্রদিগকে দান কর, তাহাতে স্বর্গে ধন পাইবে। … আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, ধনবানের পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা দুষ্কর। আবার তোমাদিগকে কহিতেছি, ঈশ্বরের রাজ্যে (স্বর্গে) ধনবানের প্রবেশ করা অপেক্ষা বরং সূচীর ছিদ্র দিয়া উটের যাওয়া সহজ।” (মথি ১৯; ২১-২৪)।
.
# ৫. কোরান
পবিত্র কোরান মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ এবং ইহা ঐশ্বরিক গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত। যে সব গ্রন্থকে ঐশ্বরিক গ্রন্থ বলিয়া দাবি করা হয়, পবিত্র কোরান তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। বরং অতুলনীয়। পবিত্র কোরানের প্রচারক হজরত মোহাম্মদ (সা.)। তিনি ৫৭১ খ্রীস্টাব্দের ২০ এপ্রিল পবিত্র মক্কা নগরে জন্মলাভ করেন এবং শৈশবেই মাতৃ-পিতৃহীন হইয়া বহু দুঃখ-কষ্টে তদীয় পিতামহ কর্তৃক প্রতিপালিত হন। শৈশবে তিনি লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পান নাই। তিনি ছিলেন আশৈশব শান্ত, ধীর, সত্যবাদী ও চিন্তাশীল। যৌবনে পদার্পণ করার সাথে সাথে তিনি হন একাধারে বিশ্বাসী, ন্যায়বান, দয়ালু, নিভীক, পরোপকারী ও ক্ষমাশীলাদি শত শত সদগুণের অধিকারী এবং ভাবুক।
সেকালের আরববাসীরা ছিল নানা দলে বিভক্ত এবং তাহাদের চরিত্র ছিল নেহায়েত মন্দ। সেকালের আরব জাহানে যদিও ইহুদি ও খ্রীস্টান ধর্মের প্রাধান্য ছিল, তবুও ঐখানে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল যথেষ্ট। মারামারি, কাটাকাটি, হিংসা, দ্বেষ, পরনিন্দা ইত্যাদি দুনিয়ার সমস্ত অন্যায়– অবিচারগুলি যেন জড়ো হইয়াছিল তখন আরবে। স্বদেশবাসীদের এহেন অধোগতি দেখিয়া ব্যথিত হইলেন হজরত মোহাম্মদ (সা.)। তিনি কেবলই চিন্তা করিতেন যে, কি করিয়া ইহাদের এই অধোগতি রোধ করা যায়, কি করিয়া ইহাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া জ্ঞানালোক দান ও একতাবদ্ধ করা যায়; কি রকমে দেখানো যায় ইহকাল ও পরকালের সরল পথ?
হজরতের বয়স যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকিল তাহার চিন্তাক্ষেত্রের পরিসর। সেই চিন্তা শুধু আরব জাহানেই সীমাবদ্ধ থাকিল না, তাহা পর্যবসিত হইল বিশ্বমানবের কল্যাণের চিন্তায়। তিনি ডুবিলেন চিন্তাসমুদ্রের গভীর তলদেশে মক্কার অদূরবর্তী হেরা পর্বতের গহ্বরে।
হজরতের বয়স তখন প্রায় ৪০ বৎসর। ৬১০ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসের ৬ তারিখ। হজরত হেরা পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্নাবস্থায় বসিয়া আছেন। এমন সময় তিনি শুনিতে পাইলেন যে, আল্লাহর ফেরেশতা জেব্রাইল আসিয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “আল্লাহর বাণী আপনার উপর নাজেল হইল, আপনি আল্লাহর রসূল।” এই দিন হইতে হজরত মোহাম্মদ (সা.) হইলেন পয়গম্বর, অর্থাৎ আল্লাহর প্রেরিত মহান বাণীবাহক।
ঐদিন হইতে হজরত তাহার সমস্যাসমূহের সমাধানে প্রাপ্ত হইতে থাকেন জেব্রাইল ফেরেশতার মারফত আল্লাহর বাণী এবং তাহা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে থাকেন ‘ভাববাণী’ রূপে। ইহকাল ও পরকাল বিষয়ে মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে আল্লাহর বাণীরূপে জেব্রাইল ফেরেশতার মারফত হজরত মোহাম্মদ (সা.) আমরণ যে সমস্ত আদেশ-উপদেশাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারই সঙ্কলন পবিত্র কোরান মহাগ্রন্থখানা।
পবিত্র কোরানের বিধান ব্যতীত হজরত স্বয়ং ধর্মজগতের আবশ্যকীয় অনেক বিধান প্রদান করিয়াছেন। সেই সমস্ত বিধানের সকলনকে বলা হয় পবিত্র হাদিস গ্রন্থ। ইসলাম ধর্ম প্রধানত পবিত্র কোরান ও হাদিস গ্রন্থের বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত।
————
৩৯. প্রাচীন মিশর, শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ১২১, ১২২।
৪০, পৃথিবীর আশ্চর্য, উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃ. ২৭।
১৬. প্লাবন ও পুনঃ সৃষ্টি
প্লাবন ও পুনঃ সৃষ্টি
মানুষ, পশু, পাখি, তরুলতা ইত্যাদি যাহা আমরা বর্তমানে দেখিতে পাইতেছি, ইহারা প্রাথমিক সৃষ্টির বংশধর নহে। জগদ্ব্যাপী এক মহাপ্লাবনের ফলে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত জীব ও উদ্ভিদাদি ধংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং গুটিকতক যাহারা জীবিত ছিল, তাহাদের বংশাবলীতে বর্তমান জগত ভরপুর।
উক্তরূপ একটি প্লাবনের কাহিনীকে কেন্দ্র করিয়া নানা দেশে নানা রকম প্রবাদ সৃষ্টি হইয়া, ঐগুলি জাতিবিশেষের মধ্যে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আছে। এইখানে আমরা উহার কয়েকটি কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।
# হিন্দুদের কাহিনী
পৌরাণিক শাস্ত্রাদিতে জলপ্লাবনের বিস্তৃত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ প্লাবনে মহর্ষি মনু যাবতীয় জীবজন্তু ও উদ্ভিদাদির বীজ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাহা হইতেই আধুনিক জীবাদির সৃষ্টি হইয়াছে।[৪১] (শতপথ ব্রাহ্মণ– প্রথম খণ্ড, অষ্টম ব্রাহ্মণ, দশম অধ্যায়; মৎস্য পুরাণ– প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়; মহাভারত– বনপর্ব, সপ্তাশীত্যধিক শততমাধ্যায় দ্রষ্টব্য)।
.
# ইরানীয়দের কাহিনী
ইরানীয়দের জেল-আভেস্তা গ্রন্থের ভেন্দিদাদ অংশে এক প্রলয়ঙ্করী প্লাবনের বিষয় লিখিত আছে। তবে উহা জলপ্লাবন নহে, তুষারপাত। উক্ত বিবরণে অহুর মজদা (ঈশ্বর) জীবাদি ধ্বংসের জন্য যিম (যম)-কে বলিতেছেন, “বিবঘতের পুত্র যিম! এই জীবজন্তু সমাকুল পৃথিবীতে ভীষণ শৈত্য উপস্থিত হইবে। তাহা হইতে সর্ববিধ্বংসী তীব্র তুষার উৎপন্ন হইয়া পৃথিবীকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। সেই তুষার পৃথিবীপৃষ্ঠে সর্বত্র বিতস্তি (১৪ অগুলি) পরিমাণ পুরু হইয়া বিদ্যমান থাকিবে। পর্বতের উচ্চ চূড়া হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদ্রের তলদেশ পর্যন্ত সমভাবে তুষারাবৃত হইবে। যে সকল প্রাণী অরণ্যে বাস করে, যাহারা পর্বতের উপর অবস্থিত থাকে, অথবা যাহারা অধিত্যকা প্রদেশে বাস করে –এই সর্বব্যাপী তুষারসম্পাতে সেই ত্রিবিধ প্রাণীই মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় লইবে। যে সকল চারণক্ষেত্র তৃণ-শল্পে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, যেখানে স্বচ্ছসলিলা স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইতেছে এবং যেখানে আজিও ক্ষুদ্র-বৃহৎ পশ্বাদি বিচরণ করিতেছে –সেই সকল স্থান হইতে, সেই ভীষণ শৈত্যাধিক্যের পূর্বে মানুষের, কুকুরের, পক্ষীর, মেষের, বৃষের বীজ সংগ্রহ করিয়া আন এবং তৎসমুদয় রক্ষার জন্য ভর প্রস্তুত করিয়া রাখ।”[৪২]
উক্ত কাহিনীটির সহিত অন্যান্য কাহিনীগুলির তিনটি বিষয়ে আপাতপার্থক্য দেখা যায়। প্রথমত, অন্যান্য কাহিনীতে পাওয়া যায় জলপ্লাবন আর এইখানে তুষারপ্লাবন। তবে জল ও তুষার মূলত একই পদার্থ। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য কাহিনীতে দেখা যায় যে, ঈশ্বর কোনো এক ব্যক্তিকে ভবিষ্যদ্ববাণী করিয়াছেন এবং অচিরেই তাহা ঘটিয়াছে; আর এইখানে উহা ঘটিয়াছে কি না, তাহার উল্লেখ নাই। বোধহয় যে, ঘটিয়া গিয়াছে। তৃতীয়ত, অন্যান্য কাহিনীতে ঈশ্বর বলিয়াছেন নৌকা তৈয়ার করিতে, আর এইখানে বলিয়াছেন ভর তৈয়ার করিতে। কিন্তু অনুবাদকগণ ‘ভর’ শব্দের অর্থ করিয়াছেন স্থান বা নৌকা। জেন্দ-আভেস্তার অনুবাদক অধ্যাপক ডারমেস্টাটর ভরকে বলিয়া গিয়াছেন নোয়ার আর্ক, অর্থাৎ নূহের নৌকা।
.
# প্রাচীন মিশরীয় ও গ্রীসবাসীদের কাহিনী
জলপ্লাবন সম্বন্ধে শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে যেরূপ বর্ণনা দৃষ্ট হয়, প্রাচীন জাতিদিগের অনেকের মধ্যেই সেইরূপ কিংবদন্তী প্রচারিত আছে। উহাতে নাম-ধামাদির পার্থক্য থাকিলেও কিছু না কিছু মিল আছেই।
মিশরীয়গণ বলেন –নুন বা নু নামক বন্যার প্রকোপে পৃথিবীর সমস্ত পদার্থের বীজ জলমগ্ন। ও নষ্ট হইয়া যায়। সেই জলপ্লাবনে ওসিরিস নামক এক ব্যক্তি রক্ষা পাইয়াছিলেন। ওসিরিস যখন আর্ক বা নৌকায় আরোহণ করেন, তখন পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। কিছুকাল পরে আলোকের উদয় হয় এবং আলোকের সঙ্গে সঙ্গে ভূখণ্ড জাগিয়া উঠে। তখন সমস্ত জীবজন্তু ও উদ্ভিদাদির বীজসহ তিনি ভূতলে অবতরণ করেন। বহি (নৌকা) হইতে অবতরণ করিয়া তিনি প্রথমে দ্রাক্ষালতা রোপণ করেন, অতঃপর মনুষ্যদিগকে কৃষিকার্য শিক্ষা দেন। ধর্ম ও নীতি বিষয়ে মনুষ্যসমাজে তিনিই প্রথম শিক্ষা প্রচার করিয়াছিলেন।
গ্রীসবাসীদের জলপ্লাবনের বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় –পৃথিবীতে পাপাচারের বৃদ্ধি দেখিয়া জিউস (গ্রীসবাসীদের ঈশ্বর) বড়ই রুষ্ট হন এবং বন্যার দ্বারা গ্রীসদেশকে প্লাবিত করেন। অত্যুচ্চ পর্বতশৃঙ্গ ভিন্ন সকলই জলমগ্ন হইয়া যায়। সেই সময় একটি আর্ক (নৌকা, মতান্তরে সিন্দুক) প্রস্তুত করিয়া ডিউকেলিয়ন সস্ত্রীক রক্ষা পাইয়াছিলেন। তাঁহার পিতা প্রমিথিউস তাহাকে জলপ্লাবন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন এবং পিতাই পুত্রকে তরণী নির্মাণ করিতে উপদেশ দেন। নয়দিন কাল জলের উপর সেই তরণী ভাসমান ছিল। অবশেষে পারনাসাস পর্বতের (ইহুদি-খ্রীস্টানরা বলেন অরারট এবং মুসলমানগণ বলেন যুদী পাহাড়) শিখরদেশে ডিউকেলিয়ন অবতরণ করেন।[৪৩]
এই সময় জিউস তাহার নিকট হারমেসকে পাঠাইয়া দেন এবং তাহাকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। ডিউকেলিয়ন তখন সেই নির্জন স্থানে মনুষ্যগণকে ও সহচরদিগকে পাঠাইয়া দিবার প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। তদনুসারে জিউস ডিউকেলিয়ন ও তাহার স্ত্রী পীঢ়া, এই উভয়কে শূন্যের দিকে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিতে বলেন। পীঢ়া যে সকল প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করেন, তাহাতে নারী জাতির সৃষ্টি হয় এবং ডিউকেলিয়নের নিক্ষিপ্ত প্রস্তর হইতে পুরুষগণ উৎপন্ন হয়। এই সময় হইতে গ্রীসে প্রস্তর যুগের লোকের অভ্যুদয় হইয়াছিল। ডিউকেলিয়ন আর্ক হইতে অবতরণ করিয়া জিউস ফিক্সিয়স অর্থাৎ পরিত্রাণকর্তা ঈশ্বরের পূজা করিয়াছিলেন।
.
# কালদিয়া ও চীনের কাহিনী
প্রাচীন কালদীয় জাতির মধ্যে জলপ্লাবনের যে বিবরণ প্রচলিত আছে, তাহাতে জানা যায় যে, ইসুগ্রাস রাজার রাজত্বকালে কালদিয়ায় জলপ্লাবন সংঘটিত হইয়াছিল। ওয়ানো নামক দেবতা সেই রাজাকে জলপ্লাবনের বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। ওয়ানো দেবতার ঊৰ্ধভাগ মনুষ্যের ন্যায়, অধোভাগ মীনসদৃশ। সেই দেবতার উপদেশে এক বৃহৎ অর্ণবপোত (নৌকা) প্রস্তুত করিয়া রাজা সপরিবারে আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। বর্তমান মনুষ্যগণ তাহারই বংশধর।
প্রাচীন চীন দেশেও জলপ্লাবনের কাহিনী প্রচারিত আছে। চীনাগণ বলেন যে, সেই ভীষণ জলপ্লাবনে মহাত্মা পয়ান সু সপরিবারে রক্ষা পাইয়াছিলেন এবং তাহাদের বংশাবলীই বর্তমান মানবগোষ্ঠী।[৪৪]
.
# সিরিয়া, কিউবা, পেরু ও ব্রাজিলের কাহিনী
সিরিয়া দেশে জলপ্লাবনের বিষয় প্রচারিত আছে। একটি গুহা দেখাইয়া প্রাচীন সিরিয়াবাসীগণ বলিতেন, এই গুহার মধ্য দিয়া সেই জলপ্লাবনের জল বাহির হইয়াছিল।
কিউবা দ্বীপে জলপ্লাবনের এবং নৌকার সাহায্যে মাত্র কয়েকজন লোকের প্রাণরক্ষার বিষয় প্রচারিত আছে।
পেরু দেশের বিবরণে প্রকাশ, পৃথিবীতে মাত্র ছয়টি মানুষ সেই জলপ্লাবনে রক্ষা পাইয়াছিল।
ব্রাজিলের বিবরণটি বেশ কৌতুকপ্রদ। এম. থেবেট তদ্বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন –কেরেবি জাতীয় সুমে একজন সভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তাহার দুই পুত্র টামেণ্ডোনের ও আরিকোন্ট। সেই দুই পুত্রের মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব ছিল না। দুই ভ্রাতা দুইরূপ প্রকৃতিসম্পন্ন ছিল। টামেণ্ডোনের শান্তিপ্রিয় ছিলেন। কিন্তু আরিকোণ্ট যুদ্ধবিগ্রহ ভালোবাসিতেন। এই হেতু উভয়ে উভয়কে ঘৃণা করিতেন এবং উভয়ে প্রায়ই বিবাদ-বিসম্বাদ ও যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিত। একদিন আপনার বল-বিক্রম দেখাইবার জন্য আরিকোন্ট আপনার সহোদরের আবাসভবনের দ্বারদেশ লক্ষ্য করিয়া অস্তনিক্ষেপ করেন। এই ঘটনায় গ্রামকে গ্রাম একেবারে আকাশে উঠিয়া যায়। টামেণ্ডোনের তখন ভূমির উপরে সজোরে আঘাত করেন। সেই আঘাতে ভূগর্ভ হইতে অবিরাম জলস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। সেই জল আকাশে মেঘমণ্ডল পর্যন্ত উচ্চ হইয়া উঠে এবং তাহাতে পৃথিবী প্লাবিত হয়। টামেণ্ডোনের ও আরিকোট দুই ভাই তখন মিলিত হইয়া পরিবারাদি সঙ্গে লইয়া এক অত্যুচ্চ পাহাড়ে আরোহণ করেন। কিছুকাল পরে জল কমিয়া আসিলে তাহারা পর্বত হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন। অবশেষে দুই ভাইয়ের দুই বংশে বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি হয়।[৪৫]
.
# ইহুদি, খ্রীস্টান ও মুসলমানদের কাহিনী
তৌরিত গ্রন্থখানা সেমিটিক জাতিরা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সকলেই মান্য করিয়া থাকেন। বিশেষত তৌরিতের আদিপুস্তক অংশে বর্ণিত প্লাবনকাহিনীটিকে সকলেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। উক্ত পুস্তকে লিখিত আছে, ঈশ্বর নোয়াকে (হজরত নূহকে) বলিতেছেন, “আর সাত দিন পরে আমি চল্লিশ দিন চল্লিশ রাত্রি অবিরাম বারিবর্ষণ করাইব, যে কোনো প্রাণী, আমি সৃষ্টি করিয়াছি, তাহাদের সমস্ত ধংসপ্রাপ্ত হইবে। পৃথিবীতে কাহারও চিহ্নমাত্র রাখিব না। সেই বৃষ্টির জল পনর হাত উচ্চ হইয়া থাকিবে” ইত্যাদি। ইহার পর ঈশ্বর নোয়াকে নৌকা প্রস্তুত করিয়া সকল প্রাণীর ও সকল সামগ্রীর বীজ তাহাতে রক্ষা করিতে উপদেশ দেন। পরমেশ্বরের আদেশমতো নোয়া নৌকা প্রস্তুত করেন এবং সেই নৌকায় পবিত্র জন্তুদিগের সাতটি পুরুষ ও সাতটি স্ত্রী এবং অপবিত্র জন্তুদিগের দুইটি পুরুষ ও দুইটি স্ত্রী গৃহীত হয়। নোয়া, নোয়ার স্ত্রী এবং হেম, শাম, জাফেট নামক তাহার পুত্রত্রয় ও তাহাদের স্ত্রীগণ সেই নৌকায় আরোহণ করিয়াছিলেন। নানা জাতীয় পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গদি সেই নৌকায় রক্ষিত হইয়াছিল। নোয়ার সেই নৌকায় রক্ষিত মনুষ্যাদি হইতে পুনরায় সংসারে পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গ ও বৃক্ষ-লতাদির উদ্ভব হইয়াছে।[৪৬]
.
# সুমেরীয় ‘গিলগামেশ’ কাহিনী
মানব সভ্যতার গোড়ার দিকে যখন সবেমাত্র লেখার প্রচলন হইয়াছে, তখন লেখা হইত কাদামাটি বা গাছের পাতায়। দূর-দূরান্তে সংবাদ আদান-প্রদানের জন্য চিঠি ও পুঁথিপত্তর পাতায়ই লেখা হইত। কোনো লেখাকে দীর্ঘস্থায়ী করিতে হইলে, উহা লেখা হইত পাথর খোদাই করিয়া। কিন্তু উহা বিস্তর শ্রম ও সময়সাপেক্ষ। পক্ষান্তরে কাদামাটির উপরে লেখা যায় সহজে, কিন্তু উহা বেশিদিন স্থায়ী হয় না। ইহার পর আবিষ্কার হইল কাদামাটির চাকতির উপর লিখিয়া ঐগুলিকে পোড়াইয়া কঠিন করা। এককালে ঐ রকম লেখার প্রচলন ছিল সুমের দেশে। তৎকালে ঐ দেশে আসুরবানিপাল নামক একজন বিদ্যোৎসাহী সম্রাট ছিলেন এবং তাহার একটি গ্রন্থাগার ছিল। কালক্রমে ঐ গ্রন্থাগারটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। অধুনা প্রত্নতাত্ত্বিকগণ উক্ত ভগ্নপটি খনন করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন আসুরবানিপালের গ্রন্থাগারটি ও তন্মধ্যে বহু মৃৎচাকতির গ্রন্থ।
বারোখানা মৃৎচাকতির উপরে লিখিত তিনশত পঙক্তি সমন্বিত গিলগামেশ নামক একখানি মহাকাব্য উদ্ধার করা হইয়াছে, তাহার কতগুলি পাওয়া গিয়াছে নিনেভের ভগ্নস্তূপমধ্যে আসুরবানিপালের গ্রন্থালয়ে। উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় স্তরে লেখা আছে একটি মহাপ্লাবনের কাহিনী।
ঐ কাহিনীটিতে বলা হইয়াছে– সুদূর অতীতে দেবতারা মানব জাতিকে ধ্বংস করার সংকল্প করিয়া পৃথিবীতে প্লাবন সৃষ্টির জন্য দেবসেনাপতি এলিনকে আদেশ দিয়াছিলেন। দৈবানুগ্রহে পূর্ব হইতে সংবাদ পাইয়া আত্মরক্ষার জন্য উৎনা পিসতিম একটি নৌকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অতঃপর বাত্যাদেবতা এনলিন যখন প্লাবন দ্বারা পৃথিবী নিমজ্জিত করিলেন, তখন উৎনা পিসতিম ও তাহার পত্নী সেই বজরায় উঠিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাহারা জীবকুলের বংশরক্ষার জন্য প্রত্যেক জাতীয় এক এক জোড়া পশু-পাখি নৌকায় তুলিয়া লইয়াছিলেন, সেই জন্যই প্রাণীজাতি ধংস পায় নাই।
একটু আয়াস স্বীকার করিয়া গিলগামেশ মহাকাব্যের প্লাবন কাহিনীর সহিত অন্যান্য দেশের কাহিনী মিলাইয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, নানান ভঙ্গির কাহিনী সত্ত্বেও উহাদের মধ্যে কিছু না কিছু মিল আছেই।
.
# মূল প্লাবন
এত অধিক প্লাবন কাহিনীর মধ্যে বিশেষ কোনো একটি সত্য, না সবগুলিই সত্য, অথবা সবগুলিই কি মিথ্যা –কয়েক বৎসর আগে পর্যন্ত এই সকল কথার সঠিক উত্তর দেওয়া কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। আলোচ্য প্লাবনের একটি চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে বর্তমান বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে মেসোপটেমিয়ার প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে। উহাতে একটি প্রচণ্ড মহাপ্লাবনের নিদর্শন ভূগর্ভে পাওয়া গিয়াছে, যাহার তুলনা সাধারণ বন্যার সঙ্গে করা চলে না। মাটির নিচে ৮ ফুট পুরু একটি পলিমাটির স্তর আবিস্কৃত হইয়াছে, যাহা অসাধারণ কোনো প্রলয়ঙ্কর প্লাবনের সাক্ষ্য দেয়। আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সুস্পষ্ট প্রমাণ এই যে, পলিস্তরটির নিচের ও উপরের মধ্যে স্থানীয় সংস্কৃতির একটি পূর্ণচ্ছেদ দেখা যায়। এই কথা সত্য যে, বন্যাপ্লাবিত স্থানগুলির সমস্ত সংস্কৃতি বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। পলিস্তরের নিচে পড়িয়া। আছে নব প্রস্তরযুগের গ্রাম্য সংস্কৃতির নিদর্শন –হাতে গড়া বিচিত্র হাঁড়ি-কুড়ি, প্রস্তরাস্ত্র; সেখানে ধাতুদ্রব্যের কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় না। কিন্তু সেই পলিস্তরের ঠিক উপরের ভাগেই ধাতুযুগের সম্পূর্ণ নূতন সভ্যতার নানাবিধ উপকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সৌভাগ্যক্রমে প্লাবিত ভূখণ্ডের কোনো কোনো স্থানে দুই সভ্যতার মধ্যে এই রকম পূর্ণচ্ছেদ দেখা যায় না। এমন কতগুলি টিলার মতো উঁচু স্থান ছিল, যাহা প্লাবনেও জলমগ্ন হয় নাই; অথচ সেই স্থানগুলি প্লাবিত ভূখণ্ডেরই অন্তর্গত। এইখানে সংস্কৃতির পূর্বাপর পারম্পর্য নষ্ট হয় নাই। নব প্রস্তরযুগ ধীরে ধীরে কিরূপে ধাতু যুগে রূপান্তরিত হইল, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস রহিয়াছে এইখানের স্তরের মধ্যে সংরক্ষিত। এই রকম স্তর হইতে আরও জানা যায় যে, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিসের নিম্নভাগে সুমের দেশে প্রস্তরযুগের গ্রামগুলি হইতেই এরেক, এরিদু, লাগাস, উর (হজরত ইব্রাহিমের জন্মস্থান), লারসা প্রভৃতি ঐতিহাসিক নগরগুলির উৎপত্তি হইয়াছিল।
প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার লিওনার্ড উলি প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছেন, “এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই যে, আমরা যে বন্যার নিশ্চিত প্রমাণ পাইয়াছি, সেই বন্যাই হইল সুমেরীয় প্রবাদকথার ও ইতিহাসের বন্যা, আবার বাইবেলেরও প্রাবন সেই বন্যা, যে বন্যাকে অবলম্বন করিয়া নোয়ার আখ্যায়িকা রচিত হইয়াছিল।”[৪৭]
————
৪১. পৃথিবীর ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ১২৮।
৪২. পৃথিবীর ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ১২৫।
৪৩. পৃথিবীর ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ১৩০, ১৩১।
৪৪. পৃথিবীর ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ১৩১।
৪৫. পৃথিবীর ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ১৩১, ১৩২।
৪৬. পৃথিবীর ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ১২৬।
৪৭. প্রাচীন ইরাক, শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ২৪-২৬, ১৮৮–১৯৩।
১৭. প্রলয়
প্রলয়
‘সৃষ্টি রহস্য’ পুস্তকে প্রলয় বা ধংস রহস্যের অবতারণা কিছু অপ্রাসঙ্গিক বোধ হয়। কিন্তু জন্মের সঙ্গে মৃত্যুর যেমন অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, সৃষ্টির সঙ্গে প্রলয়ের তেমনই। কাহারও জীবনী লিখিতে হইলে যেমন তাহার জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্তই লিখিতে হয়, নচেৎ জীবনী থাকে অসম্পূর্ণ, সৃষ্টির সঙ্গে প্রলয়ের কিছু বিবরণ না থাকিলে বোধ হয় তেমন সৃষ্টি রহস্যও থাকিবে অসম্পূর্ণ।
দিনান্তে রাত্রি, শীতান্তে গ্রীষ্ম, জন্মান্তে মৃত্যু ইত্যাদি যেমন চিরন্তন বিধি, তেমনি “সৃষ্টির শেষে প্রলয়” –ইহাতে মানুষ বিশ্বাসী। যদিও মৃত্যু একটি চিরন্তন ঘটনা, তথাপি কোনো ব্যক্তিই বলিতে পারে না যে, তাহার মৃত্যু কখন এবং কিভাবে হইবে। কিন্তু প্রলয় কখন কিভাবে হইবে, তাহা অনেকেই বলিয়া থাকেন, তবে মতামতগুলি একরূপ নহে।
সৃষ্টিরহস্যের প্রায় সমস্তই অতীতের ঘটনা, যাহা জানিবার ও বুঝিবার অনেক উপায় মানুষের আয়ত্তে আছে। যেমন –প্রত্নতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, রসায়নতত্ত্ব ইত্যাদি। কিন্তু প্রলয়রহস্যটি একেবারেই ভবিষ্যতের ব্যাপার। যেখানে অতীতকে লইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতানৈক্যের অন্ত নাই, সেখানে ভবিষ্যতকে লইয়া যে কত হাঙ্গামা, তাহা সহজেই অনুমান করা চলে। প্রলয় সম্বন্ধে বহু মতবাদ প্রচলিত আছে। এইখানে আমরা বিশেষ কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিব।
# ইরানীয়দের মত
ইরানীয়দের জেল-আভেস্তা গ্রন্থের ভেন্দিদাদ অংশে ও বুন্দেহেশ গ্রন্থে প্রলয় সম্বন্ধে লিখিত আছে, “… অবশেষে একটি জ্বলন্ত ধূমকেতু পৃথিবীতে নিপতিত হইয়া পৃথিবীকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে। গলিত ধাতুনিঃস্রাবের ন্যায় পর্বতসমূহ অগ্নত্তাপে গলিয়া যাইবে। সৎ-অসৎ সকল মনুষ্যই উত্তপ্ত বন্যাস্রোতমধ্যে ভাসিয়া ভাসিয়া পবিত্ৰীকৃত হইয়া আসিবে…” ইত্যাদি।
ধূমকেতু পতনের ফলে পৃথিবী জ্বলিয়া ও পাহাড়াদি গলিয়া যাইবে –এই যুগে উহা আর বিশ্বাস্য নহে। কেননা ধূমকেতু অতিশয় পাতলা ও হালকা বাষ্পমাত্র। ধূমকেতুর দেহে পদার্থ বলিতে কিছু নাই বলিলেই চলে। কোনো কোনো ধূমকেতুর লেজ ১০ কোটি মাইল পর্যন্ত লম্বা হইতে দেখা যায়। অথচ উহার দেহের ওজন নিতান্ত অল্প। বিজ্ঞানাচার্য জগদানন্দ রায় বলিয়াছেন, “গোটা ধূমকেতুর লেজ নিক্তিতে ওজন করিলে আধসের-তিনপোয়ার বেশি হইবে না।” (ধূমকেতুর বিশেষ বিবরণ অত্র পুস্তকের পূর্ববর্তী অংশে দ্রষ্টব্য)
.
# হিন্দুদের মত
মহাভারতের অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায়ের মার্কণ্ডেয় নারায়ণ সংবাদে সপ্তসূর্যের খরতর তাপে সংহারের ভীষণ বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই বর্ণনার কিয়দংশ এইরূপ — “সেই সহস্র চতুর্থণর অবসানে লোকের আয়ুক্ষয় সময়ে বহুবৎসর কাল অনাবৃষ্টি হইবে। … তাহাতে ভূমিষ্ঠ প্রাণীবর্গ অল্পসার ও ক্ষুধিত হইয়া পৃথিবীতে সংহারপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। তদনন্তর সপ্ত সূর্য উদিত হইয়া সরিৎ ও সরিৎপতির (নদী ও সাগরের) সমস্ত সলিল শোষণ করিতে লাগিল। শুষ্ক বা আর্দ্র যে কিছু তৃণ-কাষ্ঠ সকলই ভস্মীভূত দৃষ্ট হইতে লাগিল। তৎপরে বায়ুবাহিত সংবর্তক বহ্নি আদিত্য কর্তৃক পূর্বশোষিত পৃথিবীমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সেই অগ্নি অধঃস্থলে, নাগলোকে ও পৃথিবীতলে যে-কিছু বস্তু ছিল, তৎসমুদয় ক্ষণমধ্যে দগ্ধকরত বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। সহস্র যোজন এই জগত সেই অশুভ বায়ুসহ সংবর্তবহ্নি কর্তৃক দগ্ধ হইয়া গেল। সেই প্রদীপ্ত বিভু বহ্নিদেব অসুর, রক্ষ, গন্ধর্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষসগণের সহিত সমুদয় জগত একেবারে দগ্ধ করিয়া ফেলিল।”
মৎস্য পুরাণের দ্বিতীয় অধ্যায়েও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। সেখানে মৎস্য বলিতেছেন, “অদ্য হইতে মহীমণ্ডলে একশত বৎসর পর্যন্ত অনাবৃষ্টি হইবে। অনাবৃষ্টির ফলে অচিরেই ঘোর দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে। অনন্তর দিবাকরের সুদারুণ সপ্তরশ্মি প্রতপ্ত অঙ্গাররাশি বর্ষণকরত ক্রমশ প্রাণীগণের সংহার সাধন করিবে। যুগক্ষয়ের উপক্রম বাড়বানল বিকৃত হইবে।” ইত্যাদি।
উপরোক্ত বর্ণনায় জানা যায় যে, প্রথমত অনাবৃষ্টির ফলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে এবং তাহাতে মনুষ্যগণ মারা যাইবে। তৎপর সাতটি সূর্যের উদয় হইবে এবং তাহার তেজে নদী ও সাগরাদির জল শুকাইয়া যাইবে, বৃক্ষাদি ও প্রাণীগণ ভস্মীভূত হইবে এবং পাতালের সর্পকূল, অসুর, রক্ষ, গন্ধর্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষসগণ দগ্ধ হইয়া মারা যাইবে। হিন্দুদের দার্শনিক মতে যাহাই থাকুক, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রাদি বিশ্ববিলয়ের আলোচনা এই মতে নাই।
.
# ইহুদি ও খ্রীস্টানদের মত
পবিত্র বাইবেলের পুরাতন নিয়মের অন্তর্গত ইশিয়া নামক গ্রন্থখানা ইহুদি ও খ্রীস্টান, এই উভয় সম্প্রদায়েরই মাননীয় গ্রন্থ। ঐ গ্রন্থখানায় প্রলয় সম্বন্ধে বিবরণ এইরূপ — “সেই ভীষণ সংহারক্রিয়ার দিনে অত্যুচ্চ পর্বতসমূহ জলস্রোতে ভাসমান এবং মানুষের আবাসগৃহসমূহ ভূতলশায়ী হইবে। অধিকন্তু সেইদিন চন্দ্ররশ্মিতে সূর্যালোকের ন্যায় প্রখর জ্যোতি বিকীর্ণ করিবে। সূর্যের কিরণ বৃদ্ধি পাইবে ও সূর্যের এক দিনের তেজ সাত দিনের তেজের সমান হইবে। অর্থাৎ যেন সূর্য প্রদীপ্ত হইয়া পৃথিবীকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে।”
ইশিয়ার উল্লিখিত বিবরণটি মহাভারত ও মৎস্য পুরাণের বিবরণের সাথে কতক সাদৃশ্যপূর্ণ। মহাভারতের সূর্য সাতটি আর ইশিয়ার সূর্য একটি, কিন্তু তাহার তেজ সাতটি সূর্যের সমান।
সচরাচর একটি সূর্য হইতে আমরা যে তাপ পাইতেছি, তাহার সাত গুণ বা সাতটি সুর্যের তাপ পাইলে জীবাদি দগ্ধ হইতে পারে। কিন্তু তাহার পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, জলস্রোতে অত্যুচ্চ পর্বতমালা ভাসমান ও মানুষের গৃহাদি ভূতলশায়ী হইবে। গৃহাদি ভূতলশায়ী হইতে হইলে প্রবল বন্যা আবশ্যক এবং পাহাড়াদি ভাসাইতে যে কতটুকু জলের আবশ্যক, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। উহাতে ভূপৃষ্ঠের কোনো কিছুই অনিমগ্ন থাকিতে পারে না। পক্ষান্তরে জলমগ্ন অবস্থায় উত্তাপের মাত্রা যতই বেশি হউক না কেন, উহাতে কোনো পদার্থই দগ্ন হইতে পারে না, পারে সিদ্ধ হইতে। অতএব বুঝা যায় যে, মহাভারতের প্রলয়ে জীবাদি জ্বলিয়া পুড়িয়া অঙ্গর হইবে এবং ইশিয়ার প্রলয়ে হইবে সিদ্ধ।[৪৮]
.
# মুসলমানদের মত
মুসলমানদের মতে প্রলয় (কিয়ামত) ঘটিবার আগে দজ্জাল নামে এক ভীষণ জন্তুর আবির্ভাব। হইবে এবং পশ্চিমদিক হইতে সূর্যের উদয় হইবে। অতঃপর আল্লাহর আদেশে এস্রাফিল ফেরেশতা শিগায় ফুঁ দিবেন। শিগার ফুঁকে যুগপৎ বিকট শব্দ ও প্রলয়ঙ্করী বায়ুনিঃসারণ হইবে। উহাতে পৃথিবী কাপিয়া উঠিবে, ঘর-বাড়ি, গাছপালা, এমনকি পাহাড়াদি উড়িয়া যাইবে। এবং চন্দ্র-সূর্য ও নক্ষত্রসমূহ ধংসপ্রাপ্ত হইবে। সেই দিনের ভীষণতায় জননী শিশুকে ত্যাগ করিবে, কেহই আপন আপন মূল্যবান বা প্রিয় বস্তু ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। হিংস্র প্রাণীরা হিংস্রভাব ত্যাগ করিবে এবং পরিশেষে প্রাণ বিসর্জনে বাধ্য হইয়া সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। স্বর্গ, মর্ত, জ্বীন, ফেরেশতা কিছুই থাকিবে না, এমনকি যে এস্রাফিল ফেরেশতা শিভঙ্গ যুঁকিবেন, তিনিও না। থাকিবেন একমাত্র আল্লাহ।
.
# বিজ্ঞানীদের মত
ধর্মীয় মতে প্রলয়ের বর্ণনায় আমরা দেখিয়াছি যে, কোনো মতে লয় পাইবে শুধু জীবকুল, কোনো মতে জীবদিসহ পৃথিবী, আবার কোনো মতে লয় পাইবে পৃথিবীসহ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সবই, অবশিষ্ট থাকিবেন একমাত্র সৃষ্টিকর্তা। বিজ্ঞানীগণ প্রলয় ঘটিবার যে সমস্ত সম্ভাবনার কথা বলিয়া থাকেন, তাহার মধ্যে কয়েকটি এই —
১. কোনো কারণে যদি কখনও পৃথিবী কক্ষচ্যুত হইয়া পড়ে, তবে প্রলয়ের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ইহা সসীম। কেননা ইহাতে সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহ বা মহাবিশ্বের কোনো ক্ষতি হইবে না, ক্ষতি হইবে শুধু পৃথিবীর।
২. মহাকাশের কোনো নক্ষত্র যদি. সৌরজগতের খুব নিকটবর্তী হইয়া পড়ে, তবে সংঘর্ষের বা আকর্ষণের ফলে প্রলয় ঘটিতে পারে। কিন্তু এইরূপ কোনো ঘটনা ঘটিবে কি না, তাহার নিশ্চয়তা নাই এবং ঘটিলেও আগন্তুক নক্ষত্র ও সৌররাজ্য ব্যতীত অন্য কোনো নক্ষত্র বা মহাবিশ্বের কোনো ক্ষতি হইবে না।
৩. আলো এবং তাপের প্রধান ধর্মই হইল বিকীর্ণ হওয়া। বিকীর্ণ আলো বা তাপ কখনও তাহার উৎসক্ষেত্রে বা কেন্দ্রে ফিরিয়া আসে না, কাজেই এই অপচয় কখনও পূরণ হয় না। পৃথিবীর আলো নাই, কিন্তু তাপ আছে এবং উহা অহর্নিশ হ্রাস পাইতেছে। দৈনন্দিন পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে তাপমাত্রা কমিবার দরুন ভূপৃষ্ঠের সঙ্কোচনবশত পৃথিবীর কেন্দ্রপ্রদেশের অগ্নিময় তরল ধাতুর বিস্ফোরণ ঘটিতে পারে এবং তাহাতে পৃথিবীর অংশবিশেষ বা সমস্ত পৃথিবীও ধংস হইতে পারে, কিন্তু বিশ্বের অপর কিছু নহে।
৪. মহাবিশ্বের যাবতীয় জ্যোতিষ্ক অর্থাৎ সূর্য, নক্ষত্র, নীহারিকা ইত্যাদি সকলেই অতিশয় উষ্ণ পদার্থ এবং উহারা সকলেই নিয়ত তাপ ত্যাগ করিতেছে। জ্যোতিষ্কপুঞ্জ হইতে এইরূপ তাপ বিকিরণ হইতে হইতে এককালে এমন অবস্থা আসিতে পারে যখন মহাবিশ্বের কোথায়ও তাপের ন্যূনাধিক্য থাকিবে না। হয়তো তখন ঘটিবে বিশ্বব্যাপী মহাপ্রলয়। কিন্তু এইরূপ মহাপ্রলয় হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব না হইলেও উহা আদৌ ঘটিবে। কি না, আর ঘটিলেও তাহা কতকাল পরে ঘটিবে– কোনো বিজ্ঞানীই তাহার নিশ্চয়তা প্রদান করিতে পারেন না।
৫. এই পর্যন্ত প্রলয় সম্বন্ধে বিজ্ঞানভিত্তিক যে সমস্ত সম্ভাবনার বিষয়ে আলোচনা করা হইল, তাহার কোনোটির সম্বন্ধেই বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিতে পারেন না। ইহা ভিন্ন আর একটি সম্ভাবনা আছে, যে বিষয়ে বিজ্ঞানীগণ তাহাদের হিসাবের খাতায় অকপাত করিতে পারেন। সেইটি হইল, সৌরতেজ নিঃশেষ হইয়া সৌরজগতে প্রলয় ঘটিবার সম্ভাবনা।
বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, অন্যান্য নক্ষত্রের মতো আমাদের সূর্যও একটি নক্ষত্র। তাই ইহার জন্ম-মৃত্যু ও চরিত্রাদি অন্যান্য নক্ষত্রের মতোই। আকাশে নানা বর্ণের নক্ষত্র দেখা যায়। আকাশ বিজ্ঞানীগণ নক্ষত্রসমূহের পৃষ্ঠদেশের তাপ ও বর্ণ ভেদে নিম্নলিখিতরূপ শ্রেণীবিভাগ করেন —
বর্ণালীর শ্রেণী বর্ণ তাপমাত্রা
O অতি নীল ২০ হাজার ডিগ্রীর উপরে নীল
B নীল ১৪ হাজার ডিগ্রী
A নীলাভ শাদা ১১ হাজার ডিগ্রী
F শাদা ৭ হাজার ৪ শত ডিগ্রী
G হলুদ ৫ হাজার ৮ শত ডিগ্রী
K নারাঙ্গি ৪ হাজার ৬ শত ডিগ্রী
M লাল ৩ হাজার ২ শত ডিগ্রী
জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ বলেন যে, নক্ষত্রের বয়সের তারতম্যানুসারে উহাদের বর্ণের তারতম্য হইয়া থাকে। যে সকল নক্ষত্রের বর্ণ অতি নীল বা নীল, তাহাদের এখন পূর্ণ যৌবন এবং বয়সবৃদ্ধির সাথে সাথে বর্ণের পরিবর্তন হইয়া যথাক্রমে নীলাভ শাদা, শাদা, হলুদ ও নারাঙ্গি বর্ণ ধারণ করিয়া বার্ধক্যে হয় লাল। আকাশের লাল রঙের তারাগুলি এখন মরণপথের যাত্রী। এই লাল তারার দল আরও ঠাণ্ডা হইলে ছড়াইয়া দিবার মতো আলোর সম্বল তাহাদের ভাণ্ডারে থাকে না, তখন তাহারা আকাশে অদৃশ্য হইয়া যায়। ইহাই নক্ষত্রের মৃত্যু। এইরূপ মৃত নক্ষত্র আকাশে অনেক আছে।
কোনো কোনো বিজ্ঞানীর মতে –মহাকাশে কোনো কোনো সময় একটি মৃত নক্ষত্রের সঙ্গে আর একটি মৃত নক্ষত্রের সংঘর্ষ হয়। কেননা উহাদের আলো তাপ না থাকিলেও গতি থাকে। সংঘর্ষে উভয় নক্ষত্রের দেহ চুর্ণ-বিচুর্ণ হইয়া বাপে পরিণত হয় ও আগুন জ্বলিয়া উঠে। ফলে জন্ম হয় একটি নূতন নক্ষত্রের। নক্ষত্রদ্বয়ের দেহের আংশিক সংঘর্ষের ফলে যে আগুন জ্বলিয়া উঠে, তাহা কয়েক দিন, কয়েক মাস বা কয়েক বৎসরেই নিভিয়া যায়। কিন্তু সম্পূর্ণ গায়ে পড়া সংঘর্ষের ফলে যে আগুন জ্বলে, অর্থাৎ নক্ষত্রের জন্ম হয়, তাহা আকাশে টিকিয়া থাকে লক্ষ লক্ষ বৎসর, অতঃপর তাহাদেরও মৃত্যু। উহাদিগকে বলা হয় নেবুলা। হজরত মুসার জন্মের বৎসর মিশরবাসীরা আকাশে একটি নুতন তারা দেখিয়াছিলেন বলিয়া যে একটি প্রবাদ আছে, সম্ভবত তাহা একটি নেবুলা।
আমাদের সূর্য একটি হলুদ নক্ষত্র (G type)। ইহার বর্তমান তাপমাত্রা ৬ হাজার ডিগ্রী। নিরন্তর তাপ ও আলো ত্যাগ করিয়া উহা ক্রমে নারাঙ্গি ও পরে লাল বর্ণ ধারণ করিবে এবং তখন তাহার তাপমাত্রা দাঁড়াইবে প্রায় তিন হাজার ডিগ্রীতে। কালক্রমে যখন তাহার তাপ ও আলোর সমস্ত সম্বল ফুরাইয়া যাইবে, তখন হইবে তাহার মৃত্যু।
যে দুর্নিবার অগ্নিকাণ্ড সূর্যের ভিতর চলিতেছে, তাহার সামান্য আভাস পাই আমরা তাহার ছড়ানো তাপ ও আলোর তেজ হইতে। বিজ্ঞানীগণ বলেন, পদার্থের ন্যায় এই তেজেরও ওজন আছে। সূর্যের দেহ হইতে প্রতি সেকেণ্ডে যে পরিমাণ তেজ নিঃসৃত হয়, তাহার ওজন প্রায় ৪০ লক্ষ মণ। অর্থাৎ প্রতি সেকেণ্ডে সূর্যের ওজন ৪০ লক্ষ মণ কমিতেছে। আজ এই মুহূর্তে সূর্যের যে ওজন আছে, কাল ঠিক এই সময় তাহা হইতে ওজন কমিয়া যাইবে প্রায় ৩৫ হাজার কোটি টন। নক্ষত্রের অভ্যন্তরে যে প্রলয়কাণ্ড চলিতেছে, তাহারই আঘাতে পরমাণুর বিনাশ ঘটিয়া তেজের উদ্ভব হইতেছে। ইহাতে পরমাণু লোপ পাইয়া যে সুতীব্র তেজের সৃষ্টি হয়, তাহার ওজন ঠিক পরমাণুর ওজনের সমান। নক্ষত্রদের ভাণ্ডার এতই বিশাল যে, তাহার মধ্যে পরমাণু ধংসের উদ্দামতা বহুকাল ধরিয়া চলিতে পারে। এই অপরিমিত লোকসানেও তাহাদের রিক্ত হইতে সময় লাগে বহু কোটি বৎসর। যে পরিমাণ পরমাণুর সঞ্চয় সূর্যের আছে, তাহাতে বর্তমান লোকসানের মাত্রা বজায় রাখিয়াও সে টিকিয়া থাকিবে ১৫ লক্ষ কোটি বৎসর। অতঃপর মহানির্বাণ।
পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটিবে কিন্তু সূর্য নিভিয়া যাইবার বহু কোটি বৎসর আগেই। জন্মাবধি তাপ ত্যাগ করিয়া পৃথিবী দৈনন্দিন ঠাণ্ডা হইতে চলিয়াছে, যদিও সূর্যপ্রদত্ত তাপ প্রাপ্তির ফলে ঘাটতির পরিমাণ অল্প; কিন্তু সূর্য যখন পৃথিবীর আবশ্যকীয় তাপের জোগান দিতে পারিবে না, তখন দ্রুত তাপ ত্যাগ করিয়া পৃথিবী অত্যন্ত ঠাণ্ডা হইয়া পড়িবে। তখন পৃথিবীতে কোথাও জলের নামগন্ধও থাকিবে না, থাকিবে শুধু তুষার। তখন বাতাস বহিবে না, মেঘ হইবে না, বৃষ্টি পড়িবে না, উদ্ভিদকুল জন্মিতে বা বাঁচিতে পারিবে না –ফলে জীবকুলের হইবে অবসান। কলরববিহীন পৃথিবী অন্ধকার আকাশে ভাসিতে থাকিবে অনন্তকাল।
————
৪৮. পৃথিবীর ইতিহাস, ৩য় খণ্ড, দুর্গাদাস লাহিড়ী, পৃ. ১২৫-১৩০।
প্রলয়ের পর পুনঃ সৃষ্টি
মানুষের আশার শেষ নাই, কিন্তু উহা কোনো সময় কাজে লাগে, হয়তো কোনো সময় লাগে না। জীবজগতের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধানই হইল বাঁচিয়া থাকার আশা। স্বেচ্ছায় কেহই। মরিতে চাহে না, চাহে অমররাজ্য।
আমরা অমররাজ্যের সন্ধান পাই ভারতীয় বৈদিক সাহিত্যের বেদাদি গ্রন্থে এবং অন্যান্য ধর্মসাহিত্যে। এইখানে আমরা সেই অমরজগত সম্বন্ধে কয়েকটি মতের সামান্য আলোচনা করিব।
# বৈদিক মত
হিন্দু ধর্মকে বৈদিক ধর্মও বলা হয়। কেননা হিন্দুদের আসল ধর্মগ্রন্থ বেদ। কিন্তু বর্তমান হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রবহুল ধর্ম। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বেদের পরে গীতা, পুরাণ, উপপুরাণ ইত্যাদির রচয়িতারা বৈদিক ধর্মের গায়ে রং ফলাইয়াছেন। যে যাহা হউক, অন্যান্য মত আলোচনার পূর্বে দেখা যাক। আলোচ্য বিষয়ে ঋগ্বেদে কি পাওয়া যায়।
ঋগ্বেদের পঞ্চম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের চতুর্থ ঋকে লিখিত আছে, “মানুষ যজ্ঞ দ্বারা স্বর্গলাভে অধিকারী হয়।” যজ্ঞ কি? দেবতার উদ্দেশ্যে মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক আগুনে ঘৃত নিক্ষেপ করা। এই কাজটুকু সারিতে পারিলেই স্বর্গ নামক একটি স্থান লাভ হইবে।
ঐ বেদের ষষ্ঠ মণ্ডলের সপ্তচত্বারিংশ সূক্তের সপ্তম ঋকে ইন্দ্রদেবের নিকট প্রার্থনা করা হইতেছে, “হে ইন্দ্রদেব! তুমি আমাদিগকে সেই সুখময় ভয়শূন্য আলোকে অর্থাৎ স্বর্গলোকে লইয়া যাও।” স্বর্গ কি? উহা সুখময় আলোকিত স্থান, যেখানে কোনো বিপদ-আপদ নাই।
ঐ বেদের নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশাধিক শততম সূক্তের সপ্তম ঋকে কশ্যপ ঋষি সোম দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাইতেছেন, “যে ভুবনে সর্বদা আলোক, যে স্থানে স্বর্গলোক সংস্থাপিত আছে– হে ক্ষরণশীল! সেই অমৃত অক্ষয় ধামে আমাকে লইয়া চল।” ঋষি এইখানে এমন একটি স্থানের কামনা করিতেছেন, যেখানে দিবা আছে, রাত্রি নাই; জীবন আছে, মৃত্যু নাই এবং স্থানটির কখনও লয় নাই।
ঐ বেদের পঞ্চম মণ্ডলের পঞ্চষষ্ঠিতম সূক্তের চতুর্থ ঋকে উক্ত হইয়াছে, “মিত্র দেবতা স্তবকারীকে স্বর্গের পথ প্রদর্শন করেন।” এইখানে ঋষি মনে করিতেছেন যে, মিত্র দেব বা ভগবান তোষামোদপ্রিয়। মানুষের স্তব-স্তুতি বা প্রশংসায় তিনি তুষ্ট হন এবং স্তবকারীকে স্বর্গের পথ দেখাইয়া দেন।
ঐ মণ্ডলের ষষ্ঠষষ্ঠিতম সূক্তের ষষ্ঠ ঋকে মিত্র ও বরুণ দেবতার আহ্বানে রাত হব্য ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন, “তোমাদিগের অনুগ্রহে আমরা যেন স্বর্গধাম প্রাপ্ত হই।” এই ঋকে ঋষি মনে করিতেছেন যে, শুধু স্তব-স্তুতি, হোম-যজ্ঞ অর্থাৎ পুণ্যবলেই স্বর্গ লাভ করা যাইবে না, চাই। দেবতার দয়া।
ঐ বেদের নবম মণ্ডলের ত্রয়োদশশতাধিক শততম সূক্তের অষ্টম ঋকে বলা হইয়াছে, “সেই যে তৃতীয় নাগলোক, তৃতীয় দিব্যলোক, যাহা নভোমণ্ডলের উর্ধে আছে, যথায় ইচ্ছানুসারে বিচরণ করা যায়, যে স্থান সর্বদাই আলোকময় –তথায় আমাকে অমর কর।” ঋষি এইখানে মনে করিতেছেন যে, স্বর্গরাজ্যটি আকাশমণ্ডলের ঊর্ধ্বভাগে অবস্থিত, সেখানে অবাধে চলাফেরা করা যায়, কোনো বাধার সম্মুখীন হইতে হয় না, ঐখানে দিন-রাত্রির বালাই নাই, উহা স্বতঃস্ফুর্ত আলোকে শোভিত। তাঁহার ঐখানে বাস করা যেন স্থায়ী হয়।
ঐ মণ্ডলের নবম ঋকে ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন, “যথায় সকল কামনা নিঃশেষে পূর্ণ হয়, যথায় প্রধু নামক দেবতার ধাম আছে, যথায় যথেষ্ট আহার ও তৃপ্তিলাভ হয়– তথায় আমাকে অমর কর।” ঋষি এই ঋকে স্বর্গকে এইরূপ একটি দেশ কল্পনা করিতেছেন যে, সেখানে নৈরাশ্যের কোনো স্থান নাই এবং তৃপ্তিদায়ক প্রচুর খাদ্য পাওয়া যায়। ঋষি আশা করেন সেখানে অমর হইয়া থাকিতে।
ঐ মণ্ডলের দশম ঋকে ঋষি বলিতেছেন, “যথায় বিবিধ প্রকার আমোদ, আাদ, আনন্দ বিরাজ করিতেছে, যেখানে অভিলাষী ব্যক্তির তাবৎ কামনা পূর্ণ হয়, তথায় আমাকে অমর কর।” এই ঋকে ঋষি কল্পনা করিতেছেন যে, স্বর্গে নানাবিধ আমোদ-প্রমোদ, যথা– নাচ, গান, বাজনা ইত্যাদিও আছে এবং সেখানে নৈরাশ্যের স্থান নাই।
ঐ বেদের দশম মণ্ডলের ষোড়শ সূক্তের দ্বিতীয় ঋকে লিখিত আছে –মৃত ব্যক্তির অগ্নিসৎকার শেষ হইয়াছে; তাহার পর তাহার সম্বন্ধে বলা হইতেছে, “যখন ইনি সজীবত্বপ্রাপ্ত হইবেন, তখন দেবতাদিগের বশতাপন্ন হইবেন।” এই ঋকে বলা হইতেছে যে, মানুষ মৃত্যুর পর পুনঃ জীবিত হইবে এবং দেবগণের অধীন হইবে।
ঐ সূক্তের তৃতীয় ঋকে অগ্নি দেবতার আরাধনায় দমন ঋষি প্রার্থনা করিতেছেন, “হে জাতবেদা ও বহ্নি! তোমার যে মঙ্গলময়ী মূর্তি আছে, তাহাদিগের দ্বারা এই মৃত ব্যক্তিদিগকে পুণ্যবান লোকদিগের ভবনে বহন করিয়া লইয়া যাও।” ঋষি এইখানে চিতার আগুনকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, মৃত ব্যক্তিগণকে পুণ্যবান লোকদের ভবনে অর্থাৎ স্বর্গে লইয়া যাইতে। মনে করা হয় যে, স্বৰ্গদেশটি উদ্ধৃদিকে অর্থাৎ আকাশে অবস্থিত এবং চিতার আগুনও ঐ দিকেই যায়। সুতরাং মৃত ব্যক্তিগণকে ঐখানে পৌঁছানো অগ্নির পক্ষে অসম্ভব নহে। কিন্তু অগ্নিদেবতা পৌঁছান একই জায়গায় –পাপী ও পুণ্যবানকে।
ঐ মণ্ডলের ষষ্ঠপঞ্চাশত সূক্তের তৃতীয় ও চতুর্থ ঋকে লিখিত আছে –“যেরূপ উত্তম স্তব করিয়াছিলে, তদ্রূপ উত্তম স্বর্গে যাও।” এই ঋকে দেখা যায় যে, পুণ্যের তারতম্যের জন্য উত্তম ও অধম, ভিন্ন ভিন্ন স্বর্গ আছে।
স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে বৈদিক শিক্ষার কিছু আলোচনা করা হইল। ইহা ভিন্ন হিন্দুশাস্ত্রে আরও অনেক মত দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে এইখানে আমরা আর একটি মতের পরিচয় প্রদান করিব। এই মতে জগত তিনটি। যথা –স্বর্গ, মর্ত ও পাতাল। অর্থাৎ উর্ধলোক, মধ্যলোক ও অধোলোক। আমাদের এই পৃথিবীটিই মধ্যলোক বা মর্তলোক। এইখান হইতে উর্ধদিকে উধূলোক বা স্বর্গ। উহা সাত ভাগে বিভক্ত। যথা –ভূলোক, ভূবলোক, স্বলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক। ইহাকে সপ্তস্বর্গ বলা হয়। মর্তলোকের নিম্নদিকে অধোলোক বা পাতাল। ইহাও সাত। ভাগে বিভক্ত। যথা –অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল। ইহাকে বলা হয় সপ্তনরক। এই সপ্তনরকের অন্য নামও আছে। যথা –অম্বরীষ, রৌরব, মহারৌরব, কালসূত্র, তামিশ্র, অন্ধতামিশ্র ও অবীচি। মানুষ পুণ্যের তারতম্যানুসারে ক্রমান্বয়ে উর্ধ হইতে উর্ধতন স্বর্গের অধিকারী হয় এবং পাপের তারতম্যানুসারে নিম্ন হইতে নিম্নতম নরকে নিপতিত হয়, ইহাই এই মতের সিদ্ধান্ত। এই মতে, ত্রিজগত লয় হইবে না, লয় হইবে শুধু জীবকুল। তবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লয় ও পুনঃ সৃষ্টি হইবার মতও আছে।
হিন্দুশাস্ত্রে উক্ত আছে যে, স্বর্গরাজ্যে যাইবার পথে বৈতরণী নামক একটি নদী পার হইতে হয়। ঐ নদীর জল অগ্নিবৎ গরম, রক্ত-মাংস ও হাড়গোড়ে পরিপূর্ণ, দুর্গন্ধময় এবং কুমিরে ভরা। ঐ নদী নিরাপদে পার হইবার আশায় হিন্দুগণ মৃত্যুর পূর্বে বা পরে গো-দান করিয়া থাকেন।
হিন্দুদের কোনো কোনো শাস্ত্রে পাপ ও পুণ্যকে তুলাদণ্ডে পরিমাপ করার বিষয় বর্ণিত আছে। মহাভারতের অনুশাসন পর্বের পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ে মহর্ষি ভীষ্ম বলিতেছেন, “সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং একমাত্র সত্য তুলাদণ্ডে পরিমাপ করা হইয়াছিল, কিন্তু সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতে সত্যই ভারি হইল।”
বৈদিক মতে এতক্ষণ যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করা হইল, তাহাতে ইহাই বুঝা যায় যে, প্রলয়ান্তে পুনর্জীবন লাভ, পাপ-পুণ্যের বিচার, স্বর্গ ও নরক নামক পারলৌকিক রাজ্য, স্বর্গ-নরকের শ্রেণীবিভাগ ও সংখ্যা, শাস্তি বা পুরস্কারের বর্ণনা, স্বর্গপথে নদী পার হওয়া ইত্যাদি বিষয়সমূহ বৈদিক ও পৌরাণিক ঋষি মুনিগণ প্রচার করিয়াছিলেন।
.
# মিশরীয় মত
ভারতীয়, মিশরীয় ও ইরানীয় স্বর্গ-নরকের বর্ণনা একরূপ নহে। উহা ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষের ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ ও রুচির পরিচায়ক। ভারতীয় স্বর্গের বর্ণনায় পাওয়া যায় নন্দন কানন, পারিজাত বৃক্ষ, সুরভী গাভী, ঐবারত হস্তী, উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব ও অপ্সরা-কিন্নরী ইত্যাদি; এবং মিশরীয় স্বর্গে নাকি কৃষিকাজের ব্যবস্থাও থাকিবে।
বহুযুগ ধরিয়া প্রাচীন মিশরীয়রা প্যাপিরাস বা সমাধিগাত্রে মৃতের জীবন বিষয়ে যে সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহারই সঙ্কলন আমদুয়াত গ্রন্থ, ফটকের গ্রন্থ ও মৃতের গ্রন্থ। মৃতের গ্রন্থের মতে, প্রত্যেক মৃতকে পরমেশ্বরের কাছে একটি সত্যপাঠ (Affidavit) দিতে হয়। সত্যপাঠটি এইরূপ — “হে পরম ঈশ্বর, সত্যের ও ন্যায়ের প্রভু! তোমাকে প্রণাম। হে প্রভু! আমি তোমায় কাছে সত্যকে বহন করিয়া আসিয়াছি। আমি কোনো ব্যক্তির প্রতি অবিচার, দরিদ্রের উপর অত্যাচার, কর্তব্যকর্মে ত্রুটি ও দেবতার অনভিপ্রেত কোনো কাজ করি নাই এবং স্বাধীন মানুষকে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্বক কোনো কাজ করাই নাই … আমি পবিত্র, আমি পবিত্র।” এই সত্যপাঠটিতে প্রাচীন মিশরে প্রজার উপর রাজার, দরিদ্রের উপর ধনীর এবং গোলামের উপর মনিবের অবিচার, অত্যাচার ও জুলুমের ইঙ্গিত পাওয়া যায় (সেকালে বহু দেশেই দাসপ্রথা ছিল, কিন্তু মিশরের দাসেরা ছিল অতি উৎপীড়িত)।
ঐ সত্যপাঠ সত্য, কি মিথ্যা, তাহা যাচাই করেন জ্ঞানের দেবতা থৎ এবং হোরাস। মৃতের হৃৎপিণ্ড দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা হয়, একটি পাল্লায় ন্যায়ের প্রতীককে রাখিয়া। অতঃপর ন্যায় ও অন্যায়ের পরিমাণানুসারে মৃতকে শান্তি বা শাস্তি দেওয়া হয় (পাপ-পুণ্য পরিমাপের জন্য দাঁড়িপাল্লার ব্যবহারের বিবরণ হিন্দুশাস্ত্রেও আছে। তবে ইহা বলা যায় না যে, এই মতটির প্রথম প্রচারক আর্য ঋষিরা, না মিশরীয়রা)।
মৃতের গ্রন্থে শাস্তি বা পুরস্কারের বর্ণনা বেশি নাই। শাস্তির বিষয়ে এই মাত্র বলা হইয়াছে যে, দুষ্কৃতকারীকে কোনো ভক্ষকের কাছে দেওয়া হয়, তাহাকে ধ্বংস করার জন্য।
ফটকের গ্রন্থে বিচারদিন সম্পর্কে বর্ণনা এইরূপ — পরলোকে নানা ফটকের মধ্য দিয়া বিচার কামরায় ঢুকিতে হয়। এই বিচার কামরার সংলগ্ন দুইটি দ্বার দিয়া স্বর্গ ও নরককুণ্ডে প্রবেশ করা যায়। পুণ্যাত্মাগণ আলু নামক স্বর্গধামে যাইয়া মনের আনন্দে শস্যক্ষেত্র চাষ করে, আর পাপাত্মাদের নরককুণ্ডে পাঠাইয়া খুঁটির সঙ্গে বাধিয়া রাখা হয় –জ্বলন্ত আগুনে অথবা গভীর সমুদ্রে তাহাদের নিক্ষেপ করা হইবে বলিয়া (ইহা মিশরীয় গোলামের প্রতি মনিবের নির্মম অত্যাচারের প্রতীক)।
মৃতের গ্রন্থখানা বুক অব দি ডেড নামে ইংরাজিতে অনুদিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থের সপ্তদশ, একবিংশ ও ষড়বিংশ অধ্যায়ত্ৰয়ে মৃত ব্যক্তির স্বর্গাদিলাভ সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে, তাহার কিয়দংশের মর্ম এইরূপ — মৃত্যুর পর পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের অনুচরবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, “হে ঈশ্বরের পারিষদগণ! তোমাদের বাহু প্রসারিত করিয়া আমাকে গ্রহণ কর, আমি যেন তোমাদের মধ্যে স্থান লাভ করি। হে জ্যোতিঃস্বরূপ ওসিরিস! সম্পূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে আপনার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ। আমি করজোড়ে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনার পবিত্র আত্মায় আমাকে আশ্রয় দান করুন। আমায় স্বর্গদ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিন। মামফিসে আমার প্রতি যেরূপ আদেশ হইয়াছিল, আমি সেই আদেশ প্রতিপালন করিয়াছি। আমার হৃদয়ে এখন জ্ঞানসঞ্চার হইয়াছে …।” ঐ গ্রন্থের চতুর্দশ অধ্যায়ে লিখিত আছে, “এই মৃত ব্যক্তি নিম্নতম স্বর্গে দেবগণের অন্তর্ভুক্ত হইবেন। দেবগণ কখনোই ইহাকে পরিত্যাগ করিবেন না। কারণ ইহার আত্মা মুক্তির পথে অগ্রসর হইয়াছে। নরককীটে ইঁহাকে আর ভক্ষণ করিবে না।”
উপরোক্ত উদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে মিশরীয় স্বর্গ-নরকের স্বরূপ বুঝা যায়। অধিকন্তু উহাতে উচ্চ-নীচ স্বর্গের আভাস পাওয়া যায়। মিশরীয়গণ বিশ্বাস করিতেন যে, যুগ বিবর্তনান্তে তিন সহস্র বৎসর হইতে দশ সহস্র বৎসর পরে মৃত ব্যক্তির আত্মা দেশে ফিরিয়া আসিবে। এই বিশ্বাসের ফলেই মিশরে মৃতদেহ রক্ষার প্রথা প্রবর্তিত হয়।
.
# ইরানীয় মত
মৃত্যুর পর দণ্ড ও পুরস্কার আছে– ইরানীয়গণ ইহা বিশ্বাস করেন। মৃত্যুর পর মানুষ কি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তৎসম্বন্ধে জেন্দ-আভেস্তার ভেন্দিদাদ অংশে ও বুন্দেহেশ গ্রন্থে এইরূপ বর্ণনা আছে, “মৃত্যুর পর মানবদেহ দানবে অধিকার করে। তখন আত্মা অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকে। তৃতীয় দিবসে আত্মার জ্ঞানসঞ্চার হয়। সেই রাত্রে আত্মাকে ভীষণ চিনাভাদ নামক পুল পার হইতে হয়। যে ব্যক্তি জীবিতকালে পাপকর্ম করিয়াছে, সেতু পার হইবার সময় সে নরকার্ণবে নিপতিত হয়, আর যে ব্যক্তি চিরজীবন ধর্মানুষ্ঠানে ও সৎকাজে অতিবাহিত করিয়াছেন, সে ব্যক্তি অনায়াসে সেতু উত্তীর্ণ হইতে পারেন। যাজঙ্গণ (এক শ্রেণীর স্বর্গদূত) সৎকর্মকারীগণকে সঙ্গে করিয়া চিরশান্তিময় স্থানে (স্বর্গে) লইয়া যান। সেখানে তাহারা অহুর মজদার সহিত মিলিত হন ও স্বর্ণসিংহাসনে সমাসীন হইয়া হুরান-ই বেহিস্ত নাম্নী পরীগণের সহবাসে সর্বপ্রকার আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন।” জেন্দ-আভেস্তায় স্বর্গ-নরকের শ্রেণীবিভাগ নাই। ইরানীয়দের স্বর্গের নাম গারো-ডে মান। পারস্যভাষায় উহা গাবাৎ মান নামে অভিহিত।
যে সমস্ত পাপী সেতু পার হইতে পারে না, তাহারা দুখ নামক দুঃখার্ণবে নিপতিত হইয়া নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। তথায় দেবগণ (হিন্দুমতে দৈত্য) তাহাদিগকে অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করেন। কোন্ পাপাচারী কতদিন দুঃখার্ণবে কিরূপভাবে যন্ত্রণা ভোগ করিবে, অহুর মজদা তাহা নির্দেশ করিয়া দেন। উপাসনা দ্বারা এবং বন্ধু-বান্ধবের মধ্যস্থতায় কাহারও কাহারও দুঃখভোগের কাল হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।
ইরানীয়দের মতে, সৃষ্টির অবসানে পৃথিবী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে সওসন্ত নামক একজন অবতারের আবির্ভাব হইবে। তিনি অত্যাচার-অবিচার হইতে পৃথিবীকে মুক্ত করিবেন। তখন সেই নূতন। পৃথিবীতে অনন্ত সুখের রাজ্য সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহার পর বিশ্বব্যাপী পুনরুত্থানে বন্ধু-বান্ধব। এবং আত্মীয়-স্বজন পুনরায় মিলিত হইতে পারিবে। সেই আনন্দের সম্মিলন সংঘটিত হইলে সৎ ও অসতের মধ্যে পার্থক্য ঘটিবে। যাহারা অধর্মচারী, তাহারা ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিবে ইত্যাদি।
.
# ইহুদিদের মত
ইহুদিদিগের জুডাইজম ধর্মমতে মৃত্যুর পর বিচারের একটি শেষদিন নির্দিষ্ট আছে। সেই দিন মৃত ব্যক্তিগণের বা তাহাদের আত্মার পুনর্যুত্থান ঘটিবে। সেই দিন পাপ-পুণ্যের বিচার হইবে। কে পাপী, কে পুণ্যবান –নির্দিষ্ট একটি সেতু পার হইবার সময়েই তাহা স্থির হইয়া যাইবে (ইরানীয় মত গৃহীত)। ইহুদিগণের ধর্মগ্রন্থে পরীক্ষার দিনের বিষয়টি যেমন আছে, তেমন আছে তুলাদণ্ডে পাপ-পুণ্যের বিচারের কথা, মেশিয়া অর্থাৎ অবতারের আবির্ভাবের কথা এবং পরিশেষে চিরশান্তি প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গও। ইহুদিগণের ধর্মগ্রন্থ ওল্ড টেস্টামেন্টে প্রকাশ –“সূত্রবৎ সূক্ষ্ম সেতুর উপর। দিয়া মনুষ্যকে শেষদিনে গমন করিতে হইবে। নিম্নে ভীষণ নরক, পাপাত্মাগণ সেই সেতু হইতে নরকার্ণবে নিপতিত হইবে।” তাহাদের ধর্মগ্রন্থমতে, মানুষের পাপ-পুণ্য দুইখানি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ থাকে। শেষ বিচারের দিনে সেই দুইখানি গ্রন্থ তুলাদণ্ডের দুই দিকে রাখিয়া প্রতি জনের পাপ ও পুণ্যের পরিমাপ করা হইবে। সেই পরিমাপে পাপের ভার গুরু হইলে, পাপাত্মা নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবে; আর পুণ্যের ভাগ বেশি হইলে, পুণ্যাত্মা স্বর্গ লাভ করিবে।
ইহুদিদিগের স্বর্গের নাম ইডেন। ঐ স্বর্গ বহুমূল্য প্রস্তরে গঠিত। স্বর্গের তিনটি দ্বার। সেখানে চারিটি নদী প্রবহমানা– তাহার একটিতে দুগ্ধ, একটিতে মধু, একটিতে মদ্য এবং একটিতে সুগন্ধি নির্যাস।
স্বৰ্গকে ইহুদিগণ অতি উৎকৃষ্ট উদ্যানরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। সেই উদ্যান বহু সুমিষ্ট ফলে এবং সুগন্ধ-সুদৃশ্য ফুলে পরিপূর্ণ। সেই উদ্যান হইতে পুণ্যবানগণ ক্রমশ উচ্চ হইতে উচ্চতর স্থানের অধিকার লাভ করেন (ইহা বৈদিক সপ্তস্বর্গের অনুকরণ)।
ইহুদিদিগের ধর্মগ্রন্থ ইশিয়া, এজিকিল, ডেনিয়েল ও যব প্রভৃতিতে পুনরুত্থানের বিষয় বর্ণিত আছে। ঐ সকল গ্রন্থের কোনো কোনো স্থলে লিখিত আছে, শুষ্ক অস্থিখণ্ড পুনর্জীবিত হইয়া আপন কর্মাকর্মের ফল ভোগ করিবে; কোনো কোনো স্থানে দেখা যায়, যাহারা পৃথিবীর অভ্যন্তরে ধূলিরাশির মধ্যে নিদ্রিত হইয়া আছে, তাহারা জাগরিত হইবে। যব গ্রন্থে প্রকাশ, যেমন শরীর ছিল, সেই শরীরেই অভ্যুত্থান ঘটিবে। ইহুদিগণ বলেন, নরদেহ কবরিত হইলে, দেহের অন্যান্য অংশ ধূলায় পরিণত হয় বটে, কিন্তু লুজ নামক অস্থি বরাবর অবিকৃত থাকে। বিচারের পূর্বে পুনরুত্থানের সময়ে পৃথিবীতে ভয়ানক শিশিরপাত হইবে। সেই নীহারে সিক্ত হইয়া পূর্বোক্ত অস্থি অঙ্কুরিত অর্থাৎ নরদেহপ্রাপ্ত হইবে।
সুধী পাঠকবৃন্দের স্মরণ থাকিতে পারে যে, পবিত্র বাইবেলের আদিমানব আদমকে সৃষ্টি করিয়া তাহার বসবাসের জন্য ইডেন নামক স্বর্গে ঈশ্বর স্থান দিয়াছিলেন। ঐ স্বর্গটি কোথায় অবস্থিত, তাহার বিশেষ বিবরণ আছে তৌরিত গ্রন্থে। বিবরণটি এইরূপ — “আর সদাপ্রভু ঈশ্বর পূর্বদিকে এদনে (ইডেনে) এক উদ্যান প্রস্তুত করিলেন এবং সেই স্থানে আপনার নির্মিত ঐ মনুষ্যকে রাখিলেন। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর ভূমি হইতে সর্বজাতীয় সুদৃশ্য ও সুখাদ্যদায়ক বৃক্ষ এবং সেই উদ্যানের মধ্যস্থানে জীবনবৃক্ষ ও সদসদজ্ঞানদায়ক বৃক্ষ উৎপন্ন করিলেন। আর উদ্যানে জল সেচনার্থে এদন হইতে এক নদী নির্গত হইল। উহা তথা হইতে বিভিন্ন হইয়া চতুর্মুখ হইল। প্রথম নদীর নাম পীশোন, ইহা সমস্ত হবিলাদেশ বেষ্টন করে। তথায় স্বর্ণ পাওয়া যায় আর সেই দেশের স্বর্ণ উত্তম; এবং সেই স্থানে গুগগুলু ও গোমেদক মণি জন্মে। দ্বিতীয় নদীর নাম গীহোন, ইহা সমস্ত কুশদেশ বেষ্টন করে। তৃতীয় নদীর নাম হিদ্দেকল, ইহা অনূরিয়া দেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। চতুর্থ নদী ফরাৎ। (আদিপুস্তক ২; ৮–১৪)
উক্ত বিবরণে দেখা যায় যে, পীশোন, গীহোন, হিকেল ও ফরাং এই নদী চারিটির উৎপত্তির এলাকার মধ্যে ঐ সময় ইডেন নামে একটি জায়গা ছিল। ইডেন জায়গাটি বোধ হয় বর্তমান তুরস্ক দেশের পূর্বভাগে পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। তৌরিতে লিখিত নদী চারিটি ঐ অঞ্চল হইতেই উৎপন্ন হইয়া, পীশোন ও গীহোন নামক নদীদ্বয় কৃষ্ণসাগর ও কাস্পিয়ান সাগরে এবং হিদেকল ও ফরাৎ নামক নদীদ্বয় একত্র হইয়া পারস্য উপসাগরে পতিত হইয়াছে। ঐ ইডেন উদ্যানে বাস করাকেই বলা হয় আদমের স্বর্গবাস। আবার প্রলয়ান্তে বিচারের পর যে স্বর্গের বিবরণ পাওয়া যায় এবং তাহাতে যে দুধ, মধু, মদ ও সুগন্ধি নির্যাসে পূর্ণ নদীচতুষ্টয়ের উল্লেখ দেখা যায়, বোধ হয় যে, তাহা পূর্বোক্ত স্বৰ্গই।
.
# খ্রীস্টানদের মত
খ্রস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের (নিউ টেস্টামেন্টের) ম্যাথু, লুক, রিভিলেশন, কোরিন্থিয়ানস ও রোমানস্ প্রভৃতি অংশে পুনরুত্থানের বিষয় বিশদভাবে বিবৃত হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ –আপন পাপকর্ম দ্বারাই মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সকল মানুষই অধিক পাপে রত। সুতরাং সকলেই মৃত্যুর অধীন। মৃত্যুর পর আত্মা দেহ হইতে বিকারপ্রাপ্ত ও ধূলায় পরিণত হয়। মৃত ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাহারা পুণ্যবান, দেহত্যাগের পরেই তাহাদের আত্মা স্বর্গে গমন করে। পাপীর আত্মা শেষ বিচারের দণ্ডের জন্য প্রস্তুত হয়। শেষে একদিন তাহাদের বিচার হইরে। সেই দিন পবিত্র আত্মা যীশু খ্রীস্ট স্বর্গ হইতে মর্ত্যে অবতরণ করিবেন। স্বর্গীয় বেশে সুসজ্জিত এবং স্বর্গীয় দূত ও প্রিয় পারিষদসমূহে পরিবৃত হইয়া সেইদিন তিনি বিচারাসনে উপবিষ্ট হইবেন। মৃত ব্যক্তিগণ সেইদিন কবর হইতে উত্থিত হইবে এবং বিচারপতি প্রভু (যীশু) তাহাদের বিচার করিবেন। পাপাত্মাগণের প্রতি দণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইবে। স্বর্গীয় দূতগণ পাপীগণকে দণ্ডদানে প্রস্তুত হইবেন। পাপীদিগকে চিরপ্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইবে, তাহারা যন্ত্রণায় ছটফট করিতে থাকিবে। সেই বিচারে অতি অল্প ব্যক্তিই পুণ্যবান বলিয়া নির্দিষ্ট হইবেন। পুণ্যবানদিগকে অত্যুজ্জ্বল আলোকমালায় শোভিত প্রাসাদে লইয়া যাওয়া হইবে। সেখানে তাহারা চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় আহারাদি প্রাপ্ত হইবেন এবং সর্বসুখে সুখী থাকিবেন। তাহাদের সেই আনন্দোৎসবে তাহাদের পূর্বপুরুষগণ, অবতারগণ এবং স্বয়ং যীশুখ্রীস্ট তাহাদের সহিত যোগদান করিবেন ইত্যাদি। এই মতে বিচারকর্তা স্বয়ং ঈশ্বর নহেন, যীশু।
আলোচ্য পুস্তকসমূহে প্রলয়ান্তে পুনরুত্থান সম্বন্ধে যে সকল বিষয় লিপিবদ্ধ আছে, তাহার মর্মমাত্র এই স্থলে প্রদত্ত হইল।
.
# মুসলমানদের মত
ইসলামীয় মতে, প্রলয়ের (কেয়ামতের) চল্লিশ বৎসর (মতান্তরে চল্লিশ দিন) পরে এস্রাফিল ফেরেশতা দ্বিতীয়বার শিঙ্গা বাজাইবেন এবং পুনঃ জগত সৃষ্ট হইবে, হয়তোবা নূতন রূপে। পুনঃ সৃষ্টির পর একদিন মৃতের পুনরুত্থান হইবে। সেই দিন সকলেই আপন আপন পাপ-পুণ্যের ফল ভোগ করিবেন।
কোনো মতে, বিচারের দিনে একমাত্র আত্মাই বিচারের জন্য উপস্থিত হইবে। কিন্তু সাধারণ বিশ্বাস এই যে, সেইদিন দেহ ও আত্মা পূর্বাকারপ্রাপ্ত হইয়া বিচারপতির নিকট উপনীত হইবে। কেননা বলা হইয়া থাকে যে, বিচারক্ষেত্রে (হাশর ময়দানে) পাপীগণের হস্ত, পদ, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি পাপকর্মের সাক্ষ্য প্রদান করিবে। দোজখের শাস্তির বর্ণনায় বলা হইয়া থাকে যে, পাপীদিগকে পুঁজ-রক্ত ইত্যাদি খাইতে দেওয়া হইবে, অগ্নির উত্তাপে মস্তিষ্ক বিগলিত হইবে, যেই ব্যক্তি পরস্ত্রী দর্শন করিয়াছে, সঁড়াশীর সাহায্যে তাহার চক্ষু উৎপাটন করা হইবে এবং স্বর্গের সুখের বর্ণনায় বলা হইয়া থাকে যে, পুণ্যবানগণ নানাবিধ সুমিষ্ট ফল আহার করিবেন, নেশাহীন মদিরা পান করিবেন, হুরীসহবাস লাভ করিবেন ইত্যাদি। এই সমস্ত বর্ণনায় ও অন্যান্য ঘটনার বিবরণে পরজগতে দেহের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়া থাকে।
যে দেহ ধূলায় মিশিয়া যায়, তাহার পুনরুত্থান কিরূপে সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়া থাকে যে, সকল শরীর বিলয়প্রাপ্ত হইলেও আল-আজব (মানুষের মেরুদণ্ডের নিম্নভাগের একখানা হাড়) কখনও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না। উহ বীজম্বরূপ বিদ্যমান থাকে। পুনরুত্থানের সময়ে অন্যান্য অংশ আপনিই আসিয়া তাহার সহিত মিলিত হইবে। বিচারদিনের পূর্বে চল্লিশ দিন ব্যাপী ভীষণ বৃষ্টিপাত হইবে। সেই বৃষ্টির জলে মেরুদণ্ডের অস্থি সিক্ত হইয়া তাহা হইতে অঙ্কুরোদগমের ন্যায় নরদেহ উদগত হইবে। অতঃপর এসাফিল ফেরেশতা তৃতীয়বার শিঙ্গা ফুঁকিলে শিঙ্গায় রক্ষিত আত্মসমূহ মক্ষিকার ন্যায় ইতস্তত উড়িয়া গিয়া আপন আপন দেহে প্রবেশ করিবে ও মানুষ সজীব হইবে। সমস্ত মানবকুলের মধ্যে এইরূপ সর্বপ্রথম জীবন লাভ করিবেন হজরত মোহাম্মদ (সা.)।
পুনরুত্থানের সময় মনুষ্য, জ্বীন, ফেরেশতা ও অন্যান্য জীবজন্তু সকলেই পুনর্জীবিত হইবে এবং মানুষ ও জ্বীনগণের বিচার হইবে। কিন্তু ইতর জীবের বিচার হইবে কি না, সেই বিষয়ে মতভেদ আছে।
মনুষ্যদিগকে কোন্ রূপে বিচারপতির নিকট উপস্থিত করা হইবে, সেই বিষয়েও দ্বিমত দেখা যায়। এক মতে প্রকাশ, মাতৃগর্ভ হইতে যে অবস্থায় তাহারা ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল (নগ্নদেহে), সেই অবস্থায় তাহারা বিচারপতির নিকট উপস্থিত হইবে। অন্য মতে, যে ব্যক্তি যেরূপ বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল (বিধর্মীদের পোষাকের অনুকরণ করিয়া থাকিলে), সেইরূপ বেশভূষাতেই সে পুনরুত্থিত হইয়া বিচারার্থ প্রস্তুত থাকিবে।
কথিত হয় যে, বিচারের দিনে নানা শ্রেণীর লোক নানা অবস্থায়, কেহ ঘোড়া বা উটে চড়িয়া, কেহ হাঁটিয়া, কেহবা মাটিতে মুখ ঘষিতে ঘষিতে বিচারপতির সম্মুখে উপস্থিত হইবে।
আল্লাহ্ কোথায় বসিয়া বিচার করিবেন, সেই বিষয়ে নানা মত দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলেন যে, হজরত বলিয়া গিয়াছেন, “সিরিয়া প্রদেশে বিচারক্ষেত্র নির্দিষ্ট আছে।” কেহ বলেন, এক শ্বেত সমতল ক্ষেত্রে বিচার হইবে, সেখানে অট্টালিকা বা মনুষ্যাদির কোনো চিহ্ন নাই। অন্য মতে, সেই পৃথিবীর সহিত এই পৃথিবীর কোনো সম্বন্ধ নাই, সে এক নূতন পৃথিবী।
মুসলমানগণ বলিয়া থাকেন যে, প্রত্যেক মানুষের পাপ-পুণ্যের পরিচয়পূর্ণ একখানি পুস্তক লিখিত থাকে। পরীক্ষার দিনে সেই পুস্তক বিচারার্থীগণের হস্তে প্রদান করা হইবে। পুণ্যবান ব্যক্তিগণ ডান হস্তে সেই পুস্তক গ্রহণ করিয়া আনন্দের সহিত পাঠ করিবেন। পাপীগণের বাম হস্ত পিঠের সহিত এবং ডান হস্ত গলার সহিত বাঁধা থাকিবে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাদের বাম হস্তে বলপূর্বক সেই পুস্তক দেওয়া হইবে।
বিচারক্ষেত্রে তুলাদণ্ড থাকিবে। যে পুস্তকে পাপ-পুণ্যের কথা লিখিত হইতেছে, সেই পুস্তক তুলাদণ্ডে পরিমাপ করা হইবে। যাহার পাপের ভাগ বেশি, সে দণ্ড ভোগ করিবে এবং যাহার পুণ্যের ভাগ বেশি, সে রক্ষা পাইবে। বিচারের পর পুণ্যবানগণ স্বর্গের দিকে দক্ষিণ পথে এবং পাপীগণ নরকের দিকে বাম পথে যাইবে।
পাপী-পুণ্যবান সকলকেই আল সিরাত নামক একটি সেতু পার হইতে হইবে। সেই সেতু চুলের অপেক্ষা সূক্ষ্ম এবং তরবারির অপেক্ষা তীক্ষ্ণ ধারসম্পন্ন। নিম্নে ভীষণ অগ্নিময় নরককুণ্ড এবং উপরে ক্ষুরধার সূক্ষ্ম সেতু বিরাজমান। পুণ্যবানগণ অনায়াসে নিমেষমধ্যে সেতু পার হইয়া স্বর্গে গমন করিবেন এবং পাপীগণ পার হইবার সময়ে নরকার্ণবে পতিত হইবে।
মুসলমানদের মতে, নরকের সাতটি ভাগ এবং স্বর্গের আটটি। সাতটি নরকের (দোজখের) নাম –জাহান্নাম, লাধা, হোতামা, আল-সৈর, সাকা, আল-জাহিম ও আল-হায়াইত (হাবিয়া)। ভিন্ন ভিন্ন ধরণের পাপীগণ ভিন্ন ভিন্ন নরকে নিক্ষিপ্ত হইবে। সর্বোচ্চ পাপীর জন্য নির্ধারিত সর্বনিম্নস্থ নরক হাবিয়া। নরকের প্রতি প্রকোষ্ঠে ঊনিশ জন করিয়া প্রহরী (ফেরেশতা) আছে, প্রধান প্রহরীর নাম মালেক।
আটটি স্বর্গের (বেহেশতের) নাম– লদ, দারুস সালাম, দারুল করার, উদন, আল মাওয়া, জান্নাতুল নঈম, জান্নাতুল ইলিন ও জান্নাতুল ফেরদাউস। স্বর্গের প্রধান প্রহরীর নাম। রেজওয়ান। স্বর্গের সর্বোচ্চ স্তরের উধৃভাগে আল্লাহর আসন অবস্থিত। উহারই নিম্নভাগে সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম স্বর্গ ফেরদাউস। সেখানে সুখের অন্ত নাই। মনোহর উদ্যান, উৎস, নদী প্রভৃতি সেখানে বিরাজমান। সেখানকার নদীর কোনোটিতে পরিশ্রুত জল, কোনোটিতে দুগ্ধ, কোনোটিতে মধু, কোনোটিতে সুগন্ধী নির্যাস বহিয়া যাইতেছে। সেখানকার প্রস্তরসমূহ মুক্তা, প্রবাল ও মরকতময়। সেখানকার অট্টালিকাসমূহ স্বর্ণে বা রৌপ্যে নির্মিত। সেখানকার বৃক্ষের কাণ্ডসমূহ সুবর্ণময়।
ঐ স্বর্গে তুবা নামক একটি বৃক্ষ আছে। ঐ বৃক্ষটি সর্বসুখের আধার। স্বর্গবাসী সকলের ভবনেই সেই বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা বিস্তৃত। যিনি যেই ফলের আশা করিবেন, ঐ বৃক্ষে তিনি সেই ফলই প্রাপ্ত হইবেন।
স্বর্গে আল-কাওসার নামে একটি নদী প্রবাহিত আছে, সেরূপ সুগন্ধ ও সুস্বাদু জলে পূর্ণ নদী দ্বিতীয়টি নাই। একবার তাহার জল পান করিলে আর কখনও তৃষ্ণা পায় না।
সকল সুখের সারভূত সেখানকার হুরীগণ। অপরূপ রূপ-লাবণ্য সম্পন্ন হুরীগণ স্বর্গবাসীদিগের মনোরঞ্জনের জন্য নিযুক্ত রহিয়াছে। তাহাদের সুবৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ চক্ষু। তজ্জন্য তাহারা হুর-অল-ঐন নামে পরিচিত। মর্ত্যের রমণীগণ মৃত্তিকায় নির্মিত, কিন্তু সেই সুন্দরীবগণ মৃগনাভি দ্বারা গঠিত হইয়াছে।
.
# চৈনিক মত
কর্মানুসারে স্বর্গ-নরক লাভের এবং আত্মার অবিনশ্বরত্বের বিষয় চীনাগণও বিশ্বাস করেন। স্বর্গগত পিতৃ-পিতামহের উদ্দেশ্যে অভিবাদন চীন দেশে আবহমান কাল প্রচলিত আছে। পরলোক সম্বন্ধে চীন দেশে যে মত প্রচলিত আছে, অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার তাঁহার ‘প্রাচ্যদেশের পবিত্র গ্রন্থসমূহ’ নামক গ্রন্থের অংশবিশেষে উহার একটি পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।
খ্রী. পূ. ১৪০১ হইতে ১৩৭৪ অব্দের মধ্যে চীন দেশে পান করং নামক একজন রাজা ছিলেন। তিনি আপনার প্রজাদিগকে যে উপদেশ দেন, উপরোক্ত গ্রন্থে ম্যাক্সমূলার তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। রাজার উপদেশের মর্ম এই —
“হে প্রজাবর্গ! তোমাদিগের প্রতিপালন ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনই আমার উদ্দেশ্য। আমার পূর্বপুরুষগণ এক্ষণে আধ্যাত্মরাজ্যের অধীশ্বর। এখন কেবল তাহাদের কথাই আমার স্মৃতিপটে উদিত হইতেছে। আমার রাজ্যশাসনে যদি কোনোরূপ ভ্ৰম-প্রমাদ, ঘটে, এবং আমি যদি অধিককাল মর্তলোকে বাস করি, আমার এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সেই স্বর্গীয় নৃপতিগণ আমার দণ্ডবিধান করিবেন। আমি প্রজাদিগের প্রতি যদি কোনোরূপ অত্যাচার করি, তাহারা আমার দণ্ডবিধান করিয়া বলিবেন, “আমার প্রজাদিগের প্রতি কেন তুমি অত্যাচার করিয়াছ?” যেমন আমার সম্বন্ধে, তেমন তোমাদের সম্বন্ধে সেই স্বর্গীয় পিতৃপুরুষগণ দৃষ্টি রাখিয়াছেন। হে আমার অসংখ্য প্রজাপুঞ্জ! তোমরা যদি আমার সহিত একমত না হও, সকলে একমত হইয়া আমার মতের অনুসরণ না কর, তোমাদের জীবন চিরস্মরণীয় করিবার চেষ্টা না কর– আমার সেই স্বর্গীয় পিতৃপুরুষগণ তোমাদের সেই অপরাধের জন্য তোমাদের প্রতি কঠোর দণ্ডের বিধান করিবেন। তোমাদিগকেও আহ্বান করিয়া বলিবেন, কেন তোমরা আমাদের বংশধরের মতানুবর্তী হইতেছ না? জানিও, ইহাতে তোমাদের সকল পুণ্য ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে। রোষপরবশ হইয়া পিতৃপুরুষগণ যখন তোমাদিগের দণ্ডবিধান করিবেন, তখন তোমরা কোনোমতে রক্ষা পাইবে না। তোমাদেরও পিতৃ-পিতামহ পূর্বপুরুষগণ তখন তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন। তাহারা মৃত্যুযন্ত্রণা হইতে কদাচ তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন না।”
উপরোক্ত বিবরণে বুঝা যায় যে, স্বর্গে পিতৃপুরুষগণ বাস করেন এবং সেইখানের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা তাঁহারাই। সৎকর্মে মৃত্যুযন্ত্রণার ভয় থাকে না, অপকর্মে মৃত্যুযন্ত্রণার আশঙ্কা আছে ইত্যাদি।
সু-কিং নামক গ্রন্থখানা চীনদেশের সর্বোৎকৃষ্ট প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত। কনফুসিয়াস ঐ গ্রন্থ সকলন করিয়া যান। মৃত্যুর পর মানুষ কি অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, ঐ গ্রন্থের নানা স্থানে তাহার উল্লেখ আছে। তবে কনফুসিয়াস মৃত্যুর পরবর্তীকালের অবস্থার বিষয়ে যে কিছু বলিয়া গিয়াছেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না।
জনৈক শিষ্য কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে, তদুত্তরে কনফুসিয়াস বলিয়াছিলেন, “বর্তমান জীবনের বিষয়ই আমরা অবগত নহি, মৃত্যুর পরে কি হইবে, কে বলিতে পারে?” এতদুক্তিতে কনফুসিয়াস প্রলয়ান্তে পুনঃ সৃষ্টি বা পরলোকে বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি মৃত্যু স্বীকার করিতেন না। তাহার দর্শনানুসারে দেহাংশ পঞ্চভূত, পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে এবং অশরীরী আত্মা সংসারের মঙ্গল সাধন করিবে।
.
# বৌদ্ধ মত
খ্রী. পূ. ৫৫৬ অব্দে ভারতের কপিলাবস্তু নগরে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম। বৌদ্ধরা পরকাল বা স্বর্গ-নরকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। বৌদ্ধ মতে, জীব কামনাবশে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং জন্মে জন্মে রোগ, শোক ও নানাবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। সংসারের নানান দুঃখভোগের চিরসমাপ্তির উপায় হইল জন্ম না লওয়া। যতদিন মানুষের মনে কোনোরূপ কামনা-বাসনার লেশমাত্র থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত মানুষ পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ ও সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে থাকিবে। বিত্ত-সম্পদ ও আত্মীয়-পরিজনাদি যাবতীয় বিষয়ের তাবৎ কামনা হইতে মুক্ত হইতে পারিলে, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না। এমতাবস্থাকে বলা হয় মে এবং জন্মরহিতাবস্থাকে বলা হয় নির্বাণ।
বৌদ্ধদের ধর্মপদ নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে, “যিনি সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়াছেন, যিনি সুখ দুঃখাদিতে অভিভূত নহেন, যাহার কর্মের শেষ হইয়াছে, ভবিষ্যতে তাহার আর সংসারযন্ত্রণা ভোগের আশঙ্কা নাই। … জীবন রক্ষার এবং সুখ সাধনের অনন্ত তৃষ্ণার পরিতৃপ্তির জন্য মানুষকে জন্মে-জন্মে জরা-মৃত্যুর অধীন হইতে হইতেছে। সেই তৃষ্ণার নিবৃত্তির নামই নির্বাণ।” বৌদ্ধ মতে নির্বাণই মনুষ্য জীবনের শেষ পরিণতি। উহাতে স্বর্গ-নরক বা বিচারাদির পরিকল্পনা নাই।
মলুক্য পুত্ত নামক জনৈক ব্যক্তি বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “দেব! যিনি পূর্ণ বুদ্ধ, মৃত্যুর পর তিনি কি পুনর্জীবন লাভ করিবেন?” বুদ্ধদেব তাহাতে উত্তর দিয়াছিলেন, “এস মলুক্য পুত্ত! আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ কর। এই পৃথিবী অনন্তকাল স্থায়ী কি না, আমি তোমাকে তদ্বিষয়ে উপদেশ দিব।” মলুক্য পুত্ত কহিলেন, “আপনি তো আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না?” গৌতম বুদ্ধ উত্তর দিলেন, “হে মলুক্য পুত্ত! এই বিষয় জানিবার জন্য ব্যাকুল হইও না। যদি কোনো ব্যক্তি বিষাক্ত তীর দ্বারা বিদ্ধ হয়, আর সে যদি চিকিৎসককে বলে, কে আমার শরীরে এই তীর বিদ্ধ করিল, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কি শূদ্র, তাহা না জানিতে পারিলে আমার ক্ষতস্থানে ঔষধ প্রয়োগ করিতে দিব না –মনে কর দেখি, সেই ব্যক্তির কি পরিণাম হইবে? সেই ক্ষতই তাহার আয়ু শেষ করিবে না কি? সেইরূপ মৃত্যুর পর কি ঘটিবে জানিতে না পারায়, যে ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান লাভে এবং পবিত্র জীবন যাপনে প্রয়াস না পায়, তাহারও সেই দশা ঘটিবে। মলুক্য পুত্ত! তাই বলি, যে তত্ত্ব আজিও প্রকাশ হয় নাই, তাহা অপ্রকাশই থাকুক।”
.
# চার্বাকীয় মত
চার্বাক বৈদিক যুগের একজন দার্শনিক পণ্ডিত। কথিত আছে যে, তিনি বৃহস্পতির শিষ্য ছিলেন। চার্বাকের দার্শনিক মতটি আসলে বৃহস্পতিরই মত। বৃহস্পতির নিকট এই মত প্রাপ্ত হইয়া চার্বাক উহা সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া ঐ মতটিকে বলা হয় চার্বাক দর্শন। এই মতে –সচেতন দেহ ভিন্ন স্বতন্ত্র আত্মা নাই, পরলোক নাই, সুখই পরম পুরুষাৰ্থ, প্রত্যক্ষমাত্র প্রমাণ; মৃত্তিকা, জল, বায়ু ও অগ্নি হইতে সমস্ত পদার্থের উদ্ভব হইয়াছে ইত্যাদি।
চার্বাকের দর্শনশাস্ত্রের মূল মন্ত্র এই — “যতদিন জীবন ধারণ করা যায়, ততদিন আপনার সুখের জন্য চেষ্টা করা বিধেয়। কারণ সকলকেই একদিন কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে এবং মৃত্যুর পর এই দেহ ভস্মসাৎ হইয়া গেলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না। পরলোক বলিয়া কিছুই নাই, সুতরাং পারলৌকিক সুখলাভের প্রত্যাশায় ধর্মোপার্জনের উদ্দেশ্যে আত্মাকে ক্লেশ প্রদান করা নিতান্ত মূঢ়ের কার্য। যে দেহ একবার ভস্মীভূত হয়, তাহার পুনর্জন্ম অসম্ভব। এই স্থূল দেহই আত্মা, দেহাতিরিক্ত অন্য কোনো আত্মা নাই। ক্ষিতি, জল, বহ্নি ও বায়ু –এই চারি। ভূতের সম্মিলনে দেহের উৎপত্তি। যেমন পীতবর্ণ হরিদ্রা ও শুভ্রবর্ণ চুনের সম্মিলনে রক্তিমার। উদ্ভব হয়, অথবা যেমন মাদকতাশূন্য গুড়-তণ্ডুলাদি হইতে সুরা প্রস্তুত হইলে উহা মাদক গুণযুক্ত হয়, সেইরূপ দেহের উৎপত্তি হইলেই তাহাতে স্বভাবত চৈতন্যের বিকাশ হয়। প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ, অনুমানাদি প্রমাণ বলিয়া গণ্য নহে। উপাদেয় খাদ্য ভোজন, উত্তম বস্ত্র পরিধান, স্ত্রীসম্ভোগ প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন সুখই পরম পুরুষার্থ। এই সকল সুখের সহিত দুঃখ ভোগ করিতে হয় সত্য, কিন্তু সেই দুঃখে আস্থা প্রদর্শন না করিয়া তন্মধ্যস্থ সুখই উপভোগ করা কর্তব্য, দুঃখের ভয়ে সুখ পরিত্যাগ করা অনুচিত। কণ্টক-শল্কাদিপূর্ণ বলিয়া কে মৎস্যভক্ষণে পরামুখ হয়? তুষ দ্বারা আবৃত বলিয়া কেহ কি ধান্যকে পরিত্যাগ করে?
“প্রতারক ধূর্ত পণ্ডিতগণ আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পরলোক ও স্বর্গ-নরকাদির কল্পনা করিয়া জনসমাজকে বৃথা ভীত এবং অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। বেদ অধ্যয়ন, অগ্নিহোত্র, দণ্ডধারণ, ভস্মলেপন প্রভৃতি বুদ্ধি ও পৌরুষশূন্য ব্যক্তিবৃন্দের উপজীবিকা মাত্র। প্রতারক শাস্ত্ৰকারেরা বলে, যজ্ঞে যে জীবকে বলি প্রদান করা যায়, সেই জীবের স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। উত্তম, কিন্তু তবে তাহারা আপন আপন মাতা-পিতাকে বলি প্রদান করিয়া তাহাদিগকে স্বর্গলাভের অধিকারী করে না কেন? তাহা না করিয়া আপনাদের রসনাতৃপ্তির জন্য ছাগাদি অসহায় পশুকে বলি দেয় কেন? এইরূপে মাতা-পিতাকে স্বর্গগামী করাইতে পারিলে তজ্জন্য আর শ্রাদ্ধাদির প্রয়োজন হয় না। শ্রাদ্ধও ধূর্তদিগের কল্পনা। শ্রাদ্ধ করিলে যদি মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি হয়, তবে কোনো ব্যক্তি বিদেশে গমন করিলে তাহাকে পাথেয় না দিয়া, তাহার উদ্দেশে বাটীতে কোনো ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেই তো তাহার তৃপ্তি হইতে পারে। আর প্রাঙ্গণে শ্রাদ্ধ করিলে যখন দ্বিতলোপরিস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তি হয় না, তখন শ্রাদ্ধ দ্বারা বহু উচ্চস্থিত স্বর্গবাসীর কিরূপে তৃপ্তি হইবে? সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, শ্রাদ্ধাদিকার্য কেবল অকর্মণ্য ব্রাহ্মণদিগের জীবনোপায় ব্যতীত আর কিছুই নহে। বেদ –ভণ্ড, ধূর্ত ও রাক্ষস –এই ত্রিবিধ লোকের রচিত। স্বর্গ-নরকাদি ধূর্তের কল্পিত, আর পশুবধ ও মাংসাদি নিবেদনের বিধি রাক্ষসপ্রণীত। ‘অশ্বমেধ যজ্ঞে যজমানপত্নী অশ্বশিশ্ন (ঘোড়ার লিঙ্গ) গ্রহণ করিবে’ ইত্যাদি ব্যবস্থা ভণ্ডের রচিত। সুতরাং এই বৃথাকল্পিত শাস্ত্রে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বিশ্বাস করিতে পারেন না।
“এই দেহ ভস্মীভূত হইলে তাহার আর পুনরাগমনের সম্ভাবনা নাই। অতএব —
“যাবজ্জীবং সুখং জীবেৎ,
ঋণাং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
“অর্থাৎ যতদিন বাঁচিয়া থাকা যায়, ততদিন সুখে কালহরণ করাই কর্তব্য। এই জন্য ঋণ করিয়াও ঘৃতাদি উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য, ভোজনে পশ্চাদপদ হইবে না। এই শরীর ব্যতীত আর কোনো আত্মা নাই। যদি থাকিত এবং যদি তাহার দেহান্তর গ্রহণের ক্ষমতা থাকিত, তবে সে বন্ধু-স্বজনের স্নেহে বাধ্য হইয়া পুনর্বার ঐ দেহেই প্রবেশ করে না কি জন্য? অতএব দেখা যাইতেছে– বেদ-শাস্ত্ৰ সকলই অপ্রমাণ্য; পরলোক, স্বর্গ, মুক্তি সকলই অবান্তর; অগ্নিহোত্র, ব্রহ্মচর্য, শ্রাদ্ধাদিকর্ম সমস্তই নিষ্ফল।”
পূর্বোক্ত আলোচনায় জানা যায় যে, বৈদিক ঋষিদের পূজা-পার্বন, হোম-যজ্ঞ, শ্রাদ্ধাদি ও স্বর্গ-নরক বিষয়ক অলীক কল্পনার বিরুদ্ধে চার্বাক অভিযান চালাইয়াছিলেন সেই বৈদিক যুগেই। তবে চার্বাকের রোপিত অভিযানবৃক্ষ বিশাল আকার ধারণ করিতে পারে নাই। কিন্তু বৈদিক ধর্মের প্রবল বাত্যায় উহা নির্মূল হইয়াও যায় নাই। বৈদিকরা চার্বাকপন্থীদের বলিতেন ম্লেচ্ছ, যবন, নাস্তিক ইত্যাদি। বস্তুত চার্বাকীয় মতবাদ ছিল অভিজ্ঞতাভিত্তিক, যাহা পরবর্তীকালে আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতবাদ-এর ভিত্তিরূপে স্বীকৃত। বর্তমান জগতের বিশেষত বিজ্ঞান জগতের অনেকেই বাহ্যত না হইলেও কার্যত চার্বাকীয় মতবাদের অনুসারী।
.
# বৈজ্ঞানিক মত
অত্র পুস্তকের ‘প্রলয়’ পরিচ্ছেদে ‘বিজ্ঞানীদের মত’ আলোচনার একস্থানে বলা হইয়াছে, “মহাবিশ্বের যাবতীয় জ্যোতিষ্ক অর্থাৎ সূর্য, নক্ষত্র, নীহারিকা ইত্যাদি সকলই অতিশয় উষ্ণ পদার্থ এবং উহারা সকলেই নিয়ত তাপ বিকিরণ করিতেছে। জ্যোতিষ্কপুঞ্জ হইতে এইরূপ তাপবিকিরণ হইতে হইতে এককালে এমন অবস্থা আসিতে পারে, যখন মহাবিশ্বের কোথায়ও তাপের ন্যূনাধিক্য থাকিবে না। হয়তো তখন ঘটিবে বিশ্বজোড়া মহাপ্রলয়। কিন্তু ঐরূপ মহাপ্রলয় ঘটিলে তাহা কতকাল পরে ঘটিবে, কোনো বিজ্ঞানীই তাহার নিশ্চয়তা প্রদান করিতে পারেন নাই।”
উপরোক্ত মতে, বিশ্বের যাবতীয় নীহারিকা বা নক্ষত্ররাজ্যের প্রতিটি নক্ষত্র বা সূর্য একদিন না একদিন নিভিয়া যাইবে। তখন বিশ্বের কোথায়ও উত্তাপ বা আলোকের নামগন্ধও থাকিবে না, সর্বত্র বিরাজ করিবে কল্পনাতীত শৈত্য ও অন্ধকার। সেই হিমান্ধকার ব্যোমসমুদ্রে ভাসিতে থাকিবে নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহাদির মৃতদেহগুলি।
শৈত্যে সঙ্কুচিত ও উত্তাপে প্রসারিত হওয়া বস্তুজগতের একটি সাধারণ নিয়ম। সেই কালান্তকালের মহাশৈত্যে তখনকার বস্তুপিণ্ডগুলি সম্ভবত অতিমাত্রায় সকুচিত হইবে এবং উহার ফলে বস্তুপিণ্ডের মধ্যে প্রবল চাপের সৃষ্টি হইবে, যাহার ফলে পদার্থের পরমাণু ভাঙ্গিয়া উহা তেজ বা শক্তিতে রূপান্তরিত হইবে।
শক্তি কখনও নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারে না। তাই শক্তির সক্রিয়তার ফলে আবার শুরু হইবে (অত্র পুস্তকে লিখিত সৃষ্টির ধারা পরিচ্ছেদের বিবরণমতে) ধাপে ধাপে নূতন সৃষ্টির প্রবাহ। অর্থাৎ আবার সৃষ্টি হইতে থাকিবে ইলেকট্রন-প্রোটন, পরমাণু, নীহারিকা, নক্ষত্র, গ্রহ-উপগ্রহাদি বস্তুসমূহ, অবশেষে প্রাণ ও প্রাণী। কালান্তে আবার প্রলয় আবার সটি আবার প্রলয়। এইভাবে অনাদিকাল হইতে চলিয়াছে এবং অনন্তকাল চলিবে সৃষ্টি ও প্রলয় কাণ্ড। সুতরাং সৃষ্টি ও প্রলয় একবার-দুইবার নহে, অসংখ্যবার। অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রলয়ের কোনো আরম্ভ বা শেষ কল্পনাতীত।
১৯. উপসংহার
উপসংহার
‘সৃষ্টি রহস্য’ শেষ হইয়াও পুরাপুরি শেষ হইল না। একটি বিষয় বাকি থাকিল এইজন্য যে, তাহা শুধু সম্ভাবনাময়, তবে বাস্তবমুখী। সেই বিষয়টি হইল পৃথিবীর বাহিরে জীবন বা জীবের অস্তিত্ব।
আকাশবিজ্ঞানীদের মতে আমাদের নক্ষত্রজগতের দশ হাজার কোটি নক্ষত্রের মধ্যে একটি আমাদের সূর্য। এইখানে যে প্রক্রিয়ায় গ্রহাদি জন্মিতে পারিয়াছে, অনুরূপ প্রক্রিয়ায় অন্যান্য নক্ষত্রেও গ্রহ-উপগ্রহের জন্ম হওয়া অসম্ভব নহে এবং পৃথিবী নামক এই গ্রহটিতে যে পরিবেশে জীবন ও জীবের উদ্ভব হইয়াছে, তদনুরূপ পরিবেশে অন্যান্য নক্ষত্রের গ্রহসমূহেও জীবন ও জীবের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব নহে। হয়তো সেই সব গ্রহে মানুষের মতো বা তাহার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান প্রাণী থাকাও বিচিত্র নহে, হয়তোবা রূপান্তরে।
কোনো কোনো বিজ্ঞানীর মতে, আমাদের নক্ষত্রজগতের প্রতি একশতটি নক্ষত্রের মধ্যে একটি আমাদের সূর্যের মতো গ্রহমণ্ডল সমন্বিত। এই হিসাব মোতাবেক আমাদের নক্ষত্রজগতের দশ হাজার কোটি নক্ষত্রের মধ্যে একশত কোটি নক্ষত্রের গ্রহমণ্ডল আছে। বিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, উহাদের মধ্যে কোটি কোটি নক্ষত্রের গ্রহের তাপমাত্রা ও আবহাওয়া আমাদের পৃথিবীর মতো হইতে পারে এবং উহার অনেকগুলিতেই প্রাণ ও প্রাণীর উদ্ভব হইয়া থাকিতে পারে। অনুরূপভাবে আমাদের নক্ষত্রজগত ছাড়া আরও যে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্ৰজগত (নীহারিকা) মহাকাশে আছে, তাহাতেও গ্রহমণ্ডল সমন্বিত শত কোটি নক্ষত্র থাকিতে পারে এবং তদন্তর্গত কোটি কোটি গ্রহে জীবন বা জীবের অস্তিত্বের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করিবার কোনো কারণ নাই।
ভবিষ্যতে দূরবীনাদি পর্যবেক্ষণ যন্ত্রের আরও উন্নতি হইলে, হয়তো তখন গ্রহান্তরে জীবের বসবাসের সঠিক তথ্য জানা যাইবে এবং তখন তাহা সৃষ্টি রহস্য’-এর বিষয়সূচীর অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হইবে।
এই পুস্তকখানিতে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে মানবসমাজের কতিপয় মতবাদের কিছু কিছু আলোচনা করা হইল। ইহার মধ্যে আদিম মানবদের সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে সমালোচ্য বিষয় কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। কেননা উহা মানব জাতির শৈশব ও বাল্যকালের কল্পনা প্রসূত। কাজেই বলা যায় যে, ঐসব শিশু ও বালসুলভ উক্তি। অবশিষ্ট মতবাদসমূহের আলোচনায় দেখা যায় যে, উহাদের মধ্যে সাধারণ মতবাদ দুইটি –ধর্মীয় মতবাদ ও বৈজ্ঞানিক মতবাদ।
বিজ্ঞানীদের বলা হয় বস্তুবাদী এবং বিজ্ঞানকে বলা হয় বস্তুবাদ। আবার বিজ্ঞানকে বলা যায় গণিতের সহোদর, কেননা উভয়ের চরিত্র অভিন্ন। উহাদের কাহারও মধ্যে দয়া, মায়া, ক্ষমা, হিংসা, দ্বেষ ইত্যাদি ভাবাবেগ নাই এবং উভয়েই সত্যের পূজারী, বস্তুজগতেই উভয়ের অস্তিত্ব। যেখানে কোনো বস্তু নাই, সেখানে গণিতের প্রক্রিয়া বন্ধ, বিজ্ঞানের গবেষণা অচল। কাজেই গাণিতিকগণও বস্তুবাদী।
বর্তমান যুগে মানব সমাজের এক বিরাট এলাকা অধিকার করিয়া আছে ধর্মীয় মতবাদ তথা ভাববাদ। কিন্তু উহার সংঘাত চলিতেছে বস্তুবাদের সাথে অহরহ। ধর্মীয় মতবাদ অপরিবর্তনীয়, চিরস্থির ও স্থবির। পক্ষান্তরে বস্তুবাদ পরিবর্তনশীল, চঞ্চল ও গতিশীল। তাই বস্তুবাদের চাঞ্চল্যের গায়ে পড়া আঘাতের ভয়ে ভাববাদ আত্মরক্ষায় উদ্বিগ্ন।
ভাববাদী তপস্বীগণ যোগাসনে বসিয়া মুদ্রিত নয়নে পরমাত্মার ধ্যানে মগ্ন থাকেন আত্মোৎকর্ষ বা আত্মতৃপ্তির জন্য। তাহারা যেন মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কোনো সমস্যা দেখিতে, শুনিতে বা অনুভব করিতেই পারেন না। আর বস্তুবাদী তপস্বী (বিজ্ঞানী)-গণ তাহাদের পরীক্ষাগারেই আবদ্ধ হইয়া থাকেন না, তাহারা ছুটিয়া চলেন আকাশে, পাতালে, দেশ-দেশান্তরে; পর্যবেক্ষণ করেন বিশ্বের বৃহত্তম নক্ষত্র-নীহারিকা হইতে ক্ষুদ্রতম অণু-পরমাণু পর্যন্ত, মানবকল্যাণের জন্য।
মানব জীবনে সমস্যার অন্ত নাই। খাদ্য, বস্ত্র, রোগ ইত্যাদি অজস্র সমস্যায় মানুষ জর্জরিত। “খাদ্য সমস্যার সমাধান কি?” –এইরূপ প্রশ্ন হইলে ভাববাদীগণ বলেন, “জীব দিয়াছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি।” কিন্তু উহার জন্য বস্তুবাদীরা চক্ষু মুদিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন না। তাহারা চালাইয়া থাকেন অধিক খাদ্য ফলাও অভিযান, করেন বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানি, খোলেন অন্নসত্র। রোগাদি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইলে ভাববাদীগণ বলেন, “ঐসব ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা, উহার প্রতিকারের জন্য তাহার কাছে প্রার্থনা করাই উত্তম।” কিন্তু উহার জন্য বস্তুবাদীগণ করেন নানাবিধ ঔষধ আবিষ্কার, নির্মাণ করেন নানারূপ যন্ত্রপাতি, স্থাপন করেন নানাবিধ চিকিৎসালয়।
মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এমন কোনো বিষয় পাওয়া যায় না, যে বিষয়ে বস্তুবাদী (বিজ্ঞানী)-দের কোনোরূপ অবদান নাই। বিজ্ঞানীদের যাবতীয় সাধনার মৌলিক উদ্দেশ্য আত্মস্বার্থ বিসর্জনপূর্বক সত্যোঘাটন ও মানুষের কল্যাণ সাধন করা। তাই স্বভাবতই তাহারা ত্যাগী ও মানবপ্রেমিক। অধুনা বস্তুবাদের সহিত ত্যাগ ও প্রেম যোগে মানব জগতে গড়িয়া উঠিয়াছে এক নূতন মতবাদ, যাহার নাম মানবতাবাদ। ইহা বৈজ্ঞানিক সমাজে সমাদৃত, অনেকটা বাহিরেও। বিজ্ঞানের দুর্বার অগ্রগতি দেখিয়া মনে হয় যে, একদা মানবজগতের আন্তর্জাতিক ধর্মই হইবে মানবতাবাদ (HUMANISM)।