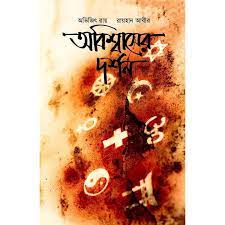- বইয়ের নামঃ অবিশ্বাসের দর্শন
- লেখকের নামঃ অভিজিৎ রায়
- বিভাগসমূহঃ দর্শন
ভূমিকা, লেখক পরিচিতি
অবিশ্বাসের দর্শন – অভিজিৎ রায় ও রায়হান আবীর
প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১১
লেখক পরিচিতি – অভিজিৎ রায় (১৯৭১– ২০১৫)
অভিজিৎ রায় যুক্তিবাদী লেখক, ব্লগার এবং মুক্তমনা ওয়েবসাইটের প্রতিষ্ঠাতা। বিজ্ঞানের সর্বশেষ তথ্যের সুসংবদ্ধ বিশ্লেষণের আলোয় লেখা ‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’, ‘মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে’, ‘সমকামিতা:একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান’, ‘শূন্য থেকে মহাবিশ্ব’ বইগুলো তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেছে বর্তমান সময়ের বিজ্ঞানমনস্ক পাঠকের অন্যতম প্রিয় লেখক হিসাবে। তার লেখা দুটি বই ‘অবিশ্বাসের দর্শন এবং বিশ্বাসের ভাইরাস মুক্তমনা মহলে ব্যাপকভাবে আলোচিত ও প্রশংসিত হয়। সুসাহিত্যিক, অনুসন্ধিৎসু, সমাজ সচেতন এবং সত্য সন্ধান ও প্রকাশে আপোষহীন অভিজিৎ রায়ের স্বপ্ন ছিলো বিজ্ঞান, মানবতাবাদ ও যুক্তিবাদের আলোকে সমাজ প্রতিষ্ঠার। সেই অর্জনের পথের সমমনাদের নিয়ে শুরু করেছিলেন মুক্তমনা ব্লগ যা আজও বাংলাভাষী বিজ্ঞানকর্মী, যুক্তিবাদী, মানবতাবাদী ও নির্ধামিকদের সবচেয়ে বড় অনলাইন সংগঠন।
অভিজিৎ রায়ের জন্ম ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সালে। তখন বাবা অধ্যাপক অজয় রায় সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে, আর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যা থেকে রক্ষা পেতে তাঁর মা শেফালি রায় আশ্রয় নিয়েছেন ভারতের আসামে। স্বাধীনতার পরে বাবার কর্মসূত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় শৈশব-কৈশোর কাটে অভিজিৎ রায়ের। তিনি যন্ত্রকৌশলে স্নাতক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। এরপরে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুর থেকে বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করে সফটওয়্যার আর্কিটেক্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন আমেরিকার আটলান্টা শহরে।
অনলাইনে অজস্র লেখালেখি ও প্রকাশিত দশটি বইয়ের মধ্যে দিয়ে অভিজিৎ অন্ধবিশ্বাস আঁকড়ে থাকা সমাজব্যবস্থার ভিত্তিমূলে আঘাত করে করে অবিরাম তুলে ধরেছেন মানবতার কথা। সাহস যুগিয়েছেন বিজ্ঞান ও যুক্তি’তে আস্থা রাখতে। ‘সমকামিতা: একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান বইটি প্রকাশিত হয় ২০০৯ সালে যার মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশের সমাজচ্যুত করে রাখা সমকামী মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন। বিজ্ঞান ও যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন মানুষের ক্ষুদ্র একটি অংশের মধ্যে সমকামী প্রবৃত্তি থাকা অপরাধ বা ক্ষতিকর নয়, বরং তা। প্রাণীজগতের স্বাভাবিক চিত্র। এর মাত্র দুই বছর পর প্রকাশিত হয় ‘অবিশ্বাসের দর্শন’ (সহ-লেখক: রায়হান আবীর) বইটি যা বিজ্ঞানপ্রিয় ও মুক্তমনা মহলে ব্যাপক আলোচিত ও প্রশংসিত হয়। এই বইটিতে আধুনিক বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে নাস্তিকতাকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে সবচেয়ে যৌক্তিক ও মানবিক অবস্থানে। ‘বিশ্বাসের ভাইরাস’ (২০১৪) বই খানিতে তিনি ধর্মকে তুলনা করেছেন ভাইরাসের সাথে এই বলে যে, ‘ধর্ম’ ব্যপারটি মানুষকে অযৌক্তিক ঈশ্বর ও অমানবিক প্রথায় বিশ্বাস স্থাপন থেকে শুরু করে আত্মঘাতী পর্যন্ত করে তুলতে পারে।
মানব মননের ক্রমাগত উন্নতিতে বিশ্বাসী অভিজিৎ রায় উৎসাহী ছিলেন বিভিন্ন বিষয়ে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায়, চিত্রকলায়, ও নারীর সামাজিক অবস্থান উন্নয়নের ভাবনাচিন্তায় সুসাহিত্যিক এবং মানবতাবাদী ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর প্রভাব নিয়ে লেখা ‘ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো: এক রবি-বিদেশিনীর খোঁজে’, অসামান্য এই বইটি প্রকাশ হয়েছিল ২০১৫ সালে। একই বছরে মহাবিশ্বের উৎপত্তি ও অস্তিত্বের সাম্প্রতিকতম ধারণা নিয়ে গণিতবিদ অধ্যাপক মীজান রহমানের সাথে লেখা ‘শূন্য থেকে মহাবিশ্ব’ বইটিও প্রকাশ পায়। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, সমাজচিন্তা, ধর্ম ও আরো বহু বিষয়ে অভিজিৎ রায়’এর লেখা কৌতূহলী-অনুসন্ধিৎসু-জিজ্ঞাসু মানুষকে যোগান দিয়েছে বস্তুবাদী চিন্তার বিপুল রসদ, যা আঘাত করেছে। আজকের পশ্চাৎগামী ও অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজের সাম্প্রদায়িক ধর্মব্যবসায়ী এবং অসৎ রাজনৈতিক সুবিধাবাদীদের’কে।
যুক্তি দিয়ে যুক্তির মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে ইসলামি জঙ্গিরা ২০১৫ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি নির্মমভাবে আক্রমণ করে অভিজিৎ রায় ও তাঁর স্ত্রী বন্যা আহমেদকে। বন্যা আহমেদ গুরুতর আহতাবস্থা থেকে বেঁচে উঠলেও সেই রাতেই অভিজিৎ রায়। মৃত্যুবরণ করেন ঢাকা মেডিকেল কলেজে। এমন নৃশংস পরিণতির বা সম্ভাবনার কথা অভিজিৎ জানতেন না তা নয়, তবু তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন ‘পাণ্ডুলিপি পোড়ে না। তাঁর সেই বিশ্বাসের অমোঘ প্রমাণ তাঁর রচনাসমূহ, যে সব আজও মানবতাবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ, প্রগতিশীল এবং মুক্তমনা প্রতিটি মানুষের জন্য প্রেরণার উৎস হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিবুদ্ধির আন্দোলনে অভিজিৎ রায় আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবেন।
তাঁর লেখা ও সম্পাদিত বই:
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী (২০০৫, অঙ্কুর প্রকাশনী)
মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে (২০০৭, অবসর প্রকাশন সংস্থা, সহলেখক: ফরিদ আহমেদ)
স্বতন্ত্র ভাবনাঃ মুক্তচিন্তা ও বুদ্ধির মুক্তি (২০০৮, অঙ্কুর প্রকাশনী, মুক্তমনা প্রবন্ধ সংকলন)।
সমকামিতা: বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান (২০১০, শুদ্ধস্বর)।
অবিশ্বাসের দর্শন (২০১১, শুদ্ধস্বর, সহলেখক: রায়হান আবীর) বিশ্বাস ও বিজ্ঞান (২০১২, অঙ্কুর প্রকাশনী, মুক্তমনা প্রবন্ধ সংকলন)
ভালবাসা কারে কয় (২০১২, শুদ্ধস্বর)
শূন্য থেকে মহাবিশ্ব (২০১৪, শুদ্ধস্বর, সহলেখক: অধ্যাপক মীজান রহমান)
বিশ্বাসের ভাইরাস (২০১৪, জাগৃতি প্রকাশনী)
ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো: এক রবি-বিদেশিনীর খোঁজে (২০১৫, অবসর প্রকাশনা সংস্থা)
.
লেখক পরিচিতি – রায়হান আবীর
রায়হান আবীর, মুক্তমনা ব্লগার। বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য নিয়ে লেখালেখি করেন। পছন্দের বিষয় বিবর্তন, পদার্থবিজ্ঞান, সংশয়বাদ। ব্লগিং করেছেন অনলাইন রাইটার্স কমিউনিটি সচলায়তন ডট কম এবং ক্যাডেট কলেজ ব্লগে। মুক্তমনা সম্পাদক অভিজিৎ রায়ের অনুপ্রেরণায় মুক্তমনা বাংলা ব্লগে বিজ্ঞান, সংশয়বাদ সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লিখছেন তিনি।
অভিজিৎ রায়ের সাথে ২০১১ সালে অমর একুশে গ্রন্থমেলায় শুদ্ধস্বর থেকে প্রকাশিত হয় প্রথম বই ‘অবিশ্বাসের দর্শন’ (দ্বিতীয় প্রকাশ: শুদ্ধস্বর ২০১২, তৃতীয় প্রকাশ: জাগতি ২০১৫), দ্বিতীয় বই ‘মানুষিকতা’ প্রকাশিত হয় শুদ্ধস্বর প্রকাশনী থেকে ২০১৩ সালে।
শৈশবের বিদ্যালয় আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ এবং এসওএস হারমান মেইনার কলেজ। কৈশোর পেরিয়েছে খাকিচত্বর বরিশাল ক্যাডেট কলেজে। ২০০৯ সালে তড়িৎ ও ইলেক্ট্রনিক প্রকৌশলে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন গাজীপুরের ইসলামিক প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (আইইউটি) থেকে। এরপর কাজ করছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োমেডিক্যাল ফিজিক্স অ্যান্ড টেকনোলজি বিভাগে।
প্রথিতযশা বিজ্ঞানী অধ্যাপক সিদ্দিক-ই-রব্বানীর নেতৃত্বে আরও একদল দেশসেরা বিজ্ঞানীর সাথে গবেষণা করে যাচ্ছেন তৃতীয় বিশ্বের মানুষের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রযুক্তি উদ্ভাবনে।
.
বরং দ্বিমত হও, আস্থা রাখো দ্বিতীয় বিদ্যায়।
বরং বিক্ষত হও প্রশ্নের পাথরে।
বরং বুদ্ধির নখে শান দাও, প্রতিবাদ করো।
অন্তত আর যাই করো, সমস্ত কথায়
অনায়াসে সম্মতি দিও না।
কেননা, সমস্ত কথা যারা অনায়াসে মেনে নেয়,
তারা আর কিছুই করে না,
তারা আত্মবিনাশের পথ
পরিষ্কার করে।
—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
.চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা
অভিজিৎ রায়ের সাথে লেখা ‘অবিশ্বাসের দর্শন বইটা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ২০১১ সালে। আমার ছোটভাই আহমেদ রেদওয়ান জান্না তখন ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। ইন্টারনেট, মোবাইল, কম্পিউটারবিহীন ওর জীবনের একমাত্র সঙ্গী ছিল ‘আউট বই। কিন্তু সে বয়সের জন্য অবিশ্বাসের দর্শন একটু বেশিই ‘আউট হয়ে যায়, তাই আমি তখন পড়ে দেখার জন্য জোর করি নি। ধর্মান্ধদের মতো আগ বাড়িযে ওকে নির্ধর্ম নিয়ে কখনও প্রেরণা দিতে ইচ্ছা করত না, কাউকেই করে না। তবে ও যেন যৌক্তিক চিন্তা করতে শেখে, সত্য মিথ্যা নির্ধারণ শিখতে পারে সে চেষ্টা করতাম সবসময়। উপযুক্ত বয়স হলে ও নিজেই সিদ্ধান্ত নেবে, কোনো প্রশ্ন আসলে উত্তর দিতে আমি তো আছি। বইটা প্রকাশিত হবার পর জান্না না পড়লেও অসম্ভব খুশি হয়েছিল তার বড় ভাই বই লিখেছে বলে, পরিবারের একমাত্র সদস্য যাকে আমি আমার লেখালেখির কথা বলতাম। প্রথম বই প্রকাশের আনন্দটা পরিবারের এই একজনের সাথেই তখন ভাগাভাগি করতে পেরেছিলাম।
দেখতে দেখতে দিন চলে যেতে থাকলো। অবিশ্বাসের দর্শনের সাথে সাথে জান্নাও বড় হতে থাকল। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ সেরে রাতে বাসায় ফিরে প্রায়ই একটু সময়ের জন্য শুয়ে থাকতাম জান্না’র বিছানায়। ও পাশের টেবিলে পড়ত। ২০১৪ সালের ত্রিশ অক্টোবর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল থেকে ঘোষিত হয় যুদ্ধাপরাধী মতিউর রহমান নিজামীর ফাঁসির রায়। এর বিরোধীতা করে যুদ্ধাপরাধী দল জামায়াত ইসলামী হরতাল ডাকে, যে কারণে স্কুলে যেতে পারে নি ও। জান্না তখন এসএসসি পরীক্ষার্থী এবং মাত্রই স্কুলের মান যাচাই পরীক্ষার তত্বীয় অংশ শেষ করেছিল। যেদিন স্কুলে যেতে পারে নি, সেদিন ওর পদার্থবিজ্ঞান ব্যবহারিক পরীক্ষা ছিল। হরতাল হলে অঘোষিত নিয়ম পরীক্ষা বাতিল। কিন্তু সেদিন হয় নি। রাতে বাসায় অভিযোগ আসলো, ব্যবহারিক পরীক্ষা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় জান্নাকে হুমকি দেওয়া হলো তাকে মূল পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না বলে। জান্না খুব মন খারাপ। করেছিল এবং ধরে নিয়েছিল ও পরিবারকে ‘অসম্মান করেছে এবং আর কখনও অসম্মান না করার উপায়ও সে বের করে ফেলে সেরাতে আত্মহত্যা করে। পরদিন সকালে দরজা ভেঙ্গে যখন ওর ঘর ঢুকি, যে ঘরটায় একসময় এক বিছানায় ঘুমাতাম আমি আর জান্না, সেই বিছানার উপরে উপরে ঝুলে আছে জান্না। তার পরনে বিবর্তনের ওপর আমার ডিজাইন করা একটা টি-শার্ট, যেটা কয়েকজন মুক্তমনা সদস্য মিলে করেছিলাম; গেঞ্জিতে লেখা ছিল- ‘বিবর্তন শুধু একটু তত্ব, ঠিক যেমন মহাকর্ষ”!
আমাদের ছেড়ে চিরতরে চলে যাবার সাত দিন আগে সে জানতে চেয়েছিল বিগব্যাং থেকে যদি আমাদের মহাবিশ্বের সূচনা হয়, তাহলে বিগব্যাং এর আগে কী ছিল? বিছানা থেকে উঠে বসে ওকে নিজে যতটুকু জানি ততটুকু ব্যাখ্যা করলাম। তারপর জানালাম ‘অবিশ্বাসের দর্শন’ বইটায় একটা অধ্যায় আছে ‘শুরুতে?” নামে, ও পড়ে দেখলে মজা পাবে। এই প্রথম ওকে বইটা পড়ে দেখতে বললাম, ওর সতেরো বছর বয়সে। অদ্ভুত হলেও সত্যি, আমার নিজের কাছে অবিশ্বাসের দর্শনের কোনো কপি ছিল না। প্রথম সংস্করণও না দ্বিতীয়টাও না। বইটা মাঝে দরকার ছিল বলে বন্ধু জামানের কপিটা নিয়ে এসেছিলাম বাসায়। জান্নাকে পড়তে দেবো ভেবে নিজের ঘরে গিয়ে বইয়ের জঙ্গলে খুঁজে দেখলাম, পেলাম না। ওকে গিয়ে বললাম, পাচ্ছি না, পরে দেবো। সে পর আর আসে নি আমার জীবনে।
প্রায় দীর্ঘদিন ‘আউট অফ প্রিন্ট’ অবিশ্বাসের দর্শন বইটি অভিজিৎ রাযের উৎসাহে প্রকাশিত হয়েছিল জাগৃতি প্রকাশনী থেকে, ২০১৫ সালের বইমেলায়। জানুয়ারির প্রথম দিনে শাহবাগে গিয়ে হাতে পেলাম নতুন ছাপা হওয়া অবিশ্বাসের দর্শন বইটি। আগৃতির প্রকাশক ফয়সাল আরেফীন দীপন ফোন করে আগের দিনই জানিয়েছিলেন যে, বইটি ছাপা হয়ে অফিসে চলে এসেছে। সত্যি বলতে কি, এই প্রথম আমি নতুন বই হাতে পেয়ে কেঁদে ফেললাম, সবচেয়ে প্রিয় মানুষকে হারিয়ে আমার জীবন যখন শূন্যতায় ভরা, তখন মনে হচ্ছিল- ইস বাসায় গিয়ে যদি জান্নাকে দেখাতে পারতাম বইটা। আমার মতো আবেগাক্রান্ত হয়েছিলেন অভিজিৎ রায়ও। যে বছরে ঘাতকরা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেবে আমাদের অভিজিৎ রায়কে সেই বছরের প্রথম দিনটা তিনি শুরু করেছিলেন ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাসের দর্শনের কথা বলে–
নববর্ষের প্রথম দিনেই প্রকাশকের কাছ থেকে একটা আনন্দের সংবাদ পেলাম। অবিশ্বাসের দর্শন বইটির তৃতীয় সংস্করণ আসছে। ছাপা শেষ, প্রচ্ছদও হয়ে গেছে। বিভিন্ন কারণেই ২০১৪ সালটি ছিল এক বিভীষিকাময় বছর। ২০১৫ সালের শুরুটা অন্ততঃ একটা আনন্দের বার্তা দিয়ে শুরু হলো, এটাই বা কম কী! ‘মুক্তি আসুক যুক্তির পথ ধরে! জীবন হোক বিশ্বাসের ভাইরাস মুক্ত”। সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা।
মায়ের গর্ভ থেকে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল অভিজিৎ রায়ের। ১৯৭১ এর উত্তাল মার্চে, তাঁর বাবা অজয় রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের শিক্ষক, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক। মুক্তিযুদ্ধ শুরুর মাত্র চার বছর আগে লীডস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিজ্ঞানে পিএইচডি এবং পোস্টডক্টরেট গবেষণা শেষ করে অজয় রায় ফিরে আসেন বাংলাদেশে, প্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। দেশে এসে শিক্ষকতা, গবেষণার পাশাপাশি সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন প্রিয় দেশকে পাকিস্তানি শোষকদের হাত থেকে রক্ষার আন্দোলনে। ১৯৭১ সালের পঁচিশে মার্চের কালো রাতে পৃথিবীর ইতিহাসের বর্বরতম হত্যাকাণ্ডের পরিকল্পনা মাথায় নিয়ে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরস্ত্র বাংলাদেশের উপর। রাত এগারোটায় ঢাকায় কারফিউ জারি করা হয়। টেলিফোন, টেলিগ্রাফসহ বাংলাদেশের সকল পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঢাকাকে আলাদা করে ফেলা হয় পুরো বাংলাদেশ থেকে। মানুষ হত্যার জন্য একের পর এক সামরিক অভিযান চলতে থাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে, রাজারবাগ পুলিশ লাইনে, ইপিআর এর সদর দফতর থেকে শুরু করে গুরুত্বপূর্ণ সব স্থানে। ট্যাঙ্ক, গ্রেনেড, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নির্বিচারে চলে সাধারণ মানুষ, ছাত্র, নারী, পুলিশ, আধা-সামরিক সদস্যদের উপর আক্রমণ। সেই ভয়ঙ্কর সময়টাতে অজয় রায়, তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী শেফালী রায় ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযের ফুলার রোডের শিক্ষকদের আবাসিক এলাকায়। ক্র্যাক ডাউনের সেই সময়ে তালিকা হাতে অজয় রায়কে হত্যার উদ্দেশ্যে হাজির হয় পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর একটি দল। সদর দরজায় নকল তালা লাগিয়ে সেরাতে পাকিস্তানী সেনাসদস্যের বোকা বানিয়ে নিজেকে, পরিবারকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন অজয় রায়। ইংল্যান্ডের চাকরি-গবেষণা-নিশ্চিত জীবনকে ঠেলে সরিয়ে যেই মানুষটি বাংলাদেশে ফিরেছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালযে যোগ দিয়েছিলেন, পরদেশের হায়েনাদের আক্রমণে সপরিবারে বাধ্য হন গৃহত্যাগে। তাঁর স্ত্রীর শেফালী রায়ের গর্ভে তখন বড়ো হচ্ছে বড়ো ছেলে অভিজিৎ রায়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসা ছেড়ে তখন ঢাকায় আত্মীয়, বন্ধুবান্ধবের বাসায় আশ্রয় নেন অজয় রায়। কারফিউ উঠে যাবার পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে সপরিবারে ঢাকা ত্যাগ করেন কুমিল্লার সোনামুড়া সীমান্ত দিয়ে। ভারতের আপার আসামে তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কমিশনে কর্মরত প্রকৌশলী বড়ো ভাইয়ের বাসায় অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে রেখে, মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণের জন্য চলে যান অজয় রায়। পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণাকে আপাতত দূরে ঠেলে কাঁধে তুলে নেন অস্ত্র, কুমিল্লা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে গেরিলা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। অজয় রায়ের সেই মুক্তিযোদ্ধা দলটির বীরত্বপূর্ণ অভিযানের কথা বর্ণনা হতে থাকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া বেতার তরঙ্গে। যুদ্ধের এক পর্যায়ে চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের নেতা এম. আর. সিদ্দীকীর পরামর্শে আগরতলা হয়ে মুজিবনগরে চলে আসেন অজয় রায়। সেখানে গিয়ে জড়িত হয়ে পড়েন তাজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত প্রবাসী স্বাধীন বাংলা সরকারের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে। অবৈতনিক সদস্য হিসেবে যোগ দেন বাংলাদেশ সরকারের প্ল্যানিং সেলে এবং পরবর্তীকালে সেক্রেটারির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।
যুদ্ধের সেই উত্তাল সময় সেপ্টেম্বরের বারো তারিখ রোববার সকাল ১২:৪২ মিনিটে শিবসাগর জেলার নাজিরাতে একটি মাতৃসেবা হাসপাতালে জন্মগ্রহণ করেন অভিজিৎ রায়। রণাঙ্গনে থাকা বাবা অজয় রায় এক স্বেচ্ছাসেবকের কাছে জানতে পারেন তার প্রথম পুত্র সন্তানের পৃথিবীতে আগমনের খবর। চাইলেই তখন ছেলের কাছে চলে যাওয়ার উপায় ছিল না তার, ছেলেকে কোলে তুলে নেবার সৌভাগ্য হয় অভিজিৎ রাযের চৌদ্দ দিন বয়সে। তারপর আবার ফিরে গিয়েছিলেন রণাঙ্গনে। ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হলে, ১১ জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে সদ্য ভূমিষ্ঠ অভিজিৎ রায়কে নিয়ে ত্রিশ লক্ষ মানুষের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন অজয় রায়। যোগ দেন কর্মস্থলে। ফিরে আসেন ফুলার রোডের বাসায়।
শিক্ষকদের আবাসিক এলাকার স্যাঁতস্যাঁতে দেওয়ালের ছোট এক বাড়িতে বেড়ে উঠতে থাকেন অভিজিৎ রায়। ছোট বেলার সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অভিজিৎ রায় লিখেছিলেন–
বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের এক ছোট্ট বাড়ির নোনাধর দ্যোল আর স্যাঁতস্যাঁতে ছাদের নীচে থেকে সেটাকেই আমরা দু-ভাই তাজমহল ভেবেছি। ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসেই ছিল উদয়ন স্কুল। সেখানে পড়তে গেছি পায়ে হেঁটে। দূরে কোথাও যেতে হলে রিক্সাই ছিল অবলম্বন। বাড়ির পাশেই বিরাট মাঠে ফুটবল ক্রিকেট খেলে কাটিয়েছি। বাবার কাছে বায়না ছিল ভালো একটা ক্রিকেট ব্যাট। আমার মনে আছে, প্রথম যখন একটা ভালো ক্রিকেট ব্যাট বাবা নিউমার্কেট থেকে কিনে দিয়েছিলেন, আনন্দে প্রায় কেঁদে ফেলেছিলাম। পরে শুনেছিলাম বাবাও নাকি ছাত্রজীবনে ক্রিকেট খেলতেন। বাবা আমাকে ‘রাজপুত্রের মতো বড়ো করতে পারেননি বটে, কিন্তু বাবাই আমাকে যত রাজ্যের বইয়ের জগতের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের শেলফে হাজারো বইয়ের পাশাপাশি ছিল মুক্তধারার কিশোর বিজ্ঞানের মজার মজার সমস্ত বই। জাফর ইকবালের ‘মহাকাশে মহাত্রাস’ কিংবা স্বপন কুমার গাযেনের ‘স্বাতীর কীর্তি’ কিংবা ‘বার্ণাডের তারা এগুলো তাঁর কল্যাণেই পড়া। বাবাই আমাকে হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন সুকুমার রাযের রচনা সমগ্র। হয়বরল এর বিড়াল, পাগলা দাশু আর হেশোরাম হুঁশিয়ারের ডায়রির কথা জেনেছি তার কাছ থেকেই। বাবাই আমার মনে বপন করেছিলেন মুক্তবুদ্ধি আর সংশয়ের প্রথম বীজ। বাবাই আমাকে আবৃত্তি করতে শিখিয়েছিলেন রবিঠাকুরের ‘প্রশ্ন’ কবিতা।
মুক্তিযুদ্ধ করে বিদেশী হায়েনাদের কাছ থেকে প্রিয় বাংলাদেশ মুক্ত হয়েছিল ঠিকই, যদিও আমাদের অনেকের মনে-প্রাণে লালিত পাকিস্তানি ভাইরাস ঠিকই রয়ে গেলো। সকল মুসলমান ভাই ভাই, এই বালখিল্য ফালতু কথার অসাড়তা আমরা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন টের পেয়েছিলাম। আমরা ধর্মীয় সকল কিছুর ঊর্ধ্বে উঠে একটি বৃহৎ মুসলমান রাষ্ট্র দ্বিখণ্ডিত করে বের হয়ে এসেছিলাম। আমরা যুদ্ধ করেছিলাম মোল্লাদের বিপক্ষে, মেয়েদের গনিমতের মাল আখ্যা দিয়ে আল্লাহর আইন দিয়ে জাস্টিফায়েড করা ধর্ষণকারীদের বিরুদ্ধে। কিন্তু সেই গৌরব কি আমরা ধরে রাখতে পেরেছি? পারি নি। ফেব্রুয়ারি, যে মাসটাকে আমি ভাবতাম ঢাকা শহরের সবচেয়ে প্রাণম্য মাস, ২০১৫ সালের সেই মাসটির ছাব্বিশ তারিখ রাতে ইসলামিক সেকুলার বাংলাদেশে চাপাতি দিয়ে হামলা করে মেরে ফেলা হয় বাংলাভাষী মুক্তচিন্তকদের সবচেয়ে বড় প্ল্যাটফর্ম মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা, বিজ্ঞান লেখক অভিজিৎ রায়কে। অভিজিৎ রায় ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী, নাস্তিক। তিনি ভালোবেসেছিলেন বিজ্ঞান, ভালোবেসেছিলেন যুক্তি। তিনি লিখেছেন বিজ্ঞান, মুক্তচিন্তা, মানবতাবাদ, সাহিত্যসহ অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ বিষযে। শুধু লেখালিখি করেই থেমে থাকেন নি তিনি, একইসাথে বাংলাদেশের মুক্তচিন্তার আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন আন্তর্জাতিক পর্যায়ে। ভাইরাসের চাপাতির আঘাতে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অভিজিৎ রায় বাংলায় লিখেছেন এবং সম্পাদনা করেছেন দশটি বই। সেরাতে অভিজিৎ রায়ের সাথে থাকা। তার স্ত্রী, মুক্তমনা সদস্য ও ‘বিবর্তনের পথ ধরে’ বইটির লেখক বন্যা আহমেদকেও কুপিয়ে আহত করা হয়, বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় তার হাতের আঙ্গুল, চাপাতি দিয়ে আঘাত করা হয় তার মাথায় এবং চোখের সামনে ধ্বংস করে দেওয়া হয় তার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ। অসহায়ের মতো বন্যা আহমেদ হারিয়ে যেতে দেখলেন তার প্রিয়তমকে আর আমরা দেখলাম আমাদের প্রিয় দাদার মাটিতে লুটিয়ে পড়ে থাকা, শুনলাম আমাদের বোনের আর্তচিৎকার, আরও দেখলাম ঢাকা মেডিকেল কলেজের মর্গের কেচিগেট। কেচিগেটের ওপারে উপুড় হয়ে শুয়ে থাকা আমার ভাই কিছুক্ষণ আগেই হাঁটছিলেন আমার বোনের হাত ধরে, হাজারো মানুষকে আপন ভেবে তারা এগিয়ে যাচ্ছিলেন সামনের দিকে, তখনও হয়ত তার মস্তিষ্কের নিউরনে লেখা হচ্ছিল নতুন কোনো প্রবন্ধ, সমাধান হচ্ছিল মুক্তমনার কারিগরি কোনো সমস্যা। আমার দাদা কিংবা বোন, আমার দেখা শ্রেষ্ঠতম মানুষ, তারা নিজেদের বদলে ভালোবেসেছিলেন তাদের দেশকে, ভালোবেসেছিলেন দেশের মানুষকে, আলোকিত করতে চেয়েছিলেন অন্ধকারাচ্ছন্ন সমাজকে। কিন্তু আলো অন্ধকারের সবচেয়ে বড়ো শত্রু, কারণ আলো জ্বালালেই দূর হয় অন্ধকার। আলোকে চাপাতি দিয়ে অন্ধকারকে কোপাতে হয় না, গুলি করতে হয় না, ঘিলু ফেলে দিতে হয় না। অন্ধকারে আলো হাতে পথ চলাই ছিল তাদের অপরাধ, আমাদের ক্ষয়ে যাওয়া সমাজে এই অপরাধ সর্বোচ্চ অপরাধ, এমন অপরাধীদের আমরা পেছন থেকে এসে হত্যা করি। কারণ আমরা অন্ধকার চাই। নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা থাকা সত্বেও সে রাতে আলো হাতে গিয়েছিলেন আমাদের আঁধারের যাত্রী, কারণ তাকে বলা হয়েছিলো বিজ্ঞান লেখকদের সাথে আড্ডার কথা। যদিও সেখানে বিজ্ঞান লেখকদের সংখ্যার তুলনায় অনেক অনেক বেশি ছিল গুপ্ত ঘাতকেরা। যারা তাকে ডেকে নিয়ে অন্ধকারের হাতে সঁপে দিয়েছিল, তারা সেদিন তার মৃত্যুতে একটুও আলোড়িত হয় নি, ক্ষুধা পেলে আমাদের যেমন খেতে হয়, তাদেরও সেরাতে ক্ষুধা মেটাতে বিরিয়ানি খেতে হয়েছে, কারও বা খেতে হয়েছে মার হাতের রাতের খাবার কিংবা অংশ নিতে হয়েছে পাঁচ তারকা হোটেলের পার্টিতে। সব শেষে তারা শান্তির নিদ্রা দিতে পেরেছে, কারও কারও সেই নিদ্রা ভাঙ্গতে লেগেছে বিশ দিন।
স্বাধীন বাংলাদেশের এক অসম্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়ে, টুপি পরে আইডিয়াল স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করে সপ্তম শ্রেণীতে চলে গেলাম থাকি চত্বরের খোঁয়াড় ক্যাডেট কলেজে। কলেজ শেষ করে মুসলমান কোটায় কোনো ভর্তি পরীক্ষা না দিয়ে ঢুকে গেলাম ইসলাম প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (আইইউটি) তে। আইইউটি, ওআইসিপরিচালিত বাংলাদেশের অন্যতম ‘আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গল্প শুনেছি তারা প্রত্যেক ছাত্রের পেছনে পনেরো হাজার ডলার ব্যয় করে শিক্ষাজীবনের চার বছরের বাজেট হিসেবে। ওআইসির সেই টাকা আমার কপালে জুটে নি, কারণ মুসলমান হলেও ভালো মুসলিম ছাত্র ছিলাম না, বাবা-মার পকেট থেকে মোটা অংকের টিউশন ফি দিয়েই তাই পড়াশোনা করতে হয়েছে।
আইইউটিতে ভর্তি হবার আগেই জানতাম এখানে কেবলমাত্র ‘মানুষ’ (শর্ত প্রযোজ্য) দের ভর্তি হবার সুযোগ দেওয়া হয়। ‘মুসলিম পুরুষ’ হওয়াটাই সেখানে মানুষ হবার একমাত্র শর্ত। আইইউটির দুয়ার নারী এবং অমুসলিমদের জন্য বন্ধ। এই চরম সাম্প্রদায়িক আচরণ আমাকে অবাক করলেও অন্য সবার কাছে শুনেছি- জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে মুসলমানদের অবস্থা সারাবিশ্বেই খুব খারাপ, মুসলমানরা নিজেরা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করে নিজেরা পড়াশোনা করে নিজেদের উন্নতি সাধনের চেষ্টা নাকি খুব ভালো। নারীদের ঢুকতে না দেওয়ার উছিলাটা ছিল- তাতে করে নাকি বিশ্ববিদ্যালয় জুড়ে শুধু পাপাচার হবে। প্রথম বর্ষেই আমাদের তৎকালীন তড়িৎ প্রকৌশল বিভাগের প্রধান পাকিস্তানি অধ্যাপক বলেছিলেন ঠিক এই কথাটাই। রুমে ইন্টারনেট সংযোগ দেওয়ার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতেও তার যুক্তি ইসলাম ধর্মে প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে যাবার পর ভাই আর বোনেরও এক রুমে থাকা নিষিদ্ধ। ইন্টারনেটও ঠিক তেমন একটি প্রাপ্ত বয়স্ক আপন বোন, রুমে তাকে আমাদের সাথে একা রাখা যাবে না।
২০০৭ সাল। দ্বিতীয় বর্ষের সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা শেষে দীর্ঘ তিনমাসের ছুটি চলছে। আমার বাসায় থাকতে ভালো লাগত না, তাই ছুটির সময়েও হলে থাকতাম। সপ্তাহান্তে ছোট ভাই জান্নাকে দেখতে খুব ইচ্ছা হতো। ও তখন ক্লাস টু এর পুচকা এবং প্রতি সপ্তাহের শুক্রবারে আমাকে দেখতে পেলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেত কারণ আমাকে বললেই আমি চকলেট, আইসক্রিম আর কোক খাওয়াতাম। গাজীপুর থেকে জ্যাম ঠেলে ঢাকা আসতে তিন ঘণ্টা সময় লাগে। সেই সময় আমার প্রথম পরিচয় হয় ‘অভিজিৎ রায় এর লেখার সাথে। প্রিয় বন্ধু ‘শিক্ষানবিস’ আজিজ মার্কেট থেকে দুটো বই কিনে এনেছিল। ‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’ এবং ‘মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে’। শিক্ষানবিস ময়মনসিংহের এক লাইব্রেরিতে আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী বইটির সামান্য অংশ পড়ে অভিজিৎ রাযের লেখনীতে বেশ মুগ্ধ হয়েছিল, তাই আজিজ থেকে ‘আস্ত” দু’টি বই কিনে আনা। পরের সপ্তাহান্তে জান্নাকে দেখার জন্য আলো। হাতে আঁধারের যাত্রীকে সঙ্গী করে জ্যাম হাতে বাসযাত্রী হলাম। সেই থেকে শুরু। অভিজিৎ রায়ের আলোয় কাল্পনিক সত্তার দাসত্ব থেকে মুক্ত জীবন।
আমাদের সমাজ সদ্যজন্মজাত শিশুর ইহলৌকিক খেলার মাঠের মৌলিক চাহিদা পূরণে খুব একটা আগ্রহী না হলেও তার। পরকাল নিশ্চিত করতে সিদ্ধহস্ত। জন্মগ্রহণ করতে না করতেই সে একটি নির্দিষ্ট ধর্মযুক্ত হয়ে যায়, তারপর ধীরে ধীরে তাকে শেখানো হয় সে যে দলভুক্ত তারাই সেরা, একমাত্র সত্যপথের অনুসারী। অন্যান্যদের জন্য রয়েছে…… (কী রয়েছে সেটা দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করুন)। আমার ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। ছোটবেলা থেকেই আশেপাশের সবার কাছে আমার ধর্মের মুজেজা শুনেছি, আর ভেবেছি ‘ওয়াও!!”। আমার বন্ধু-বান্ধব কেউ অন্য কোনো ধর্মের অনুসারী ছিল কিনা এখন মনে নেই, থাকলেও তাদের সাথে ধর্ম সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার কথা হয়নি নিশ্চিত। হলে তখনই জানতে পারতাম, নিজ ধর্মকে অন্যদের চেয়ে সেরা প্রতীয়মান করার জন্য প্রত্যেক ধর্মই নানা ধরনের আকর্ষণীয় মুজেজা সংবলিত গল্পের আশ্রয় নেয়। এই সহজ সত্যটা বোধহয় পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই না জেনে ইন্তেকাল করেন।
আমিও হয়ত সে পথেই যাচ্ছিলাম। ক্যাডেট কলেজে কোনো এক শুক্রবার আমাদের মসজিদের ঈমাম, আবেগঘন ওয়াজ করতে করতে এক গল্প শোনালেন। সে গল্পে ঈশ্বরের অসীম কুদরতে বিখ্যাত কোনো ব্যক্তির পাতে থাকা ভাজা মাছ হঠাৎ করে অভাজা মাছ হয়ে পানিতে ঝাঁপ দিয়ে থর্পের মতো সাঁতার কেটে হারিয়ে যায় গভীর জলে। সমসাময়িক আর আট-দশটা ছেলের মতই বাংলাদেশি মুসলমান পরিবারে বডো হবার ফলে তখনও আমি নিজেকে ধার্মিক ভাবতাম, যদিও পালন করতাম না সেভাবে। ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হতে পারলে ‘মানত” করেছিলাম সেখানে ছয় বছর এক ওয়াক্ত নামাজ বাদ দেবো না। সেটা সম্ভব হয় নি। যদিও কোনো ঝামেলায়পড়লে আর রহমান সুরা এগারো বার পড়ে আল্লাহর নিকট ঝামেলা মুক্তির আবেদন করতাম এ আশায় যে এগারো বার ‘সুরা আর রহমান’ পড়লে যেকোনো ধরনের ঝামেলা থেকে প্যারোলে মুক্তি পাওয়ার বিষয়টা একেবারেই অব্যর্থ। এছাড়া পাশের বাড়ির কোনো মেয়েকে ভালো লাগলেও ‘আর রহমান এবং সুরা ইয়াসিনের আশ্রয় নিতাম, কারণ সুরাগুলো যথাক্রমে এগারোবার ও তিনবার পড়লে, মনোবাসনা পূরণ হতে বাধ্য। কিন্তু ভাজা মাছের জ্যান্ত হয়ে যাওয়া বিশ্বাস করা অসম্ভব। মনে মনে ভাবলাম- যদি সত্যিকার অর্থেই এমন ঘটনা কোরান হাদিসে থেকে থাকে, তবুও আমি ভাজা মাছের অভাজা হয়ে যাওয়া বিশ্বাস করতে পারব না। ধন্যবাদ।
কিন্তু তাতে করে কোনো কিছুই বদলায় না। কোরান মহাসত্য গ্রন্থ এবং আল্লাহ এক এবং তিনি শুধু আমাদের দলে। এমন করে কেটে যেতে থাকা সময়ে একদিন কাঁটাবন মসজিদের লাইব্রেরিতে একটা বই দেখলাম। ইসলাম ও বিজ্ঞান বিষয়ে জনৈক ‘আহমদ দীদাত’ এর লেখা। সে বইয়ে ‘মিরাকল নাইন্টিন” নিয়ে একটি অধ্যায় ছিল- যা পড়ে আল্লাহ এবং বিশেষ করে কোরান যে অলৌকিক গ্রন্থ সে ব্যাপারে একেবারে নিঃসংশয় হয়ে গেলাম। ‘রাস্তা ঠিকাছে, এখন শুধু ঠিকঠাক ড্রাইভ করে বেহেশতে পৌঁছাতে হবে, তারপরইইইই …”। তখন বাংলা উইকিপিডিয়াতে সময় পেলেই নতুন নতুন নিবন্ধ তৈরি করি। বইটা পড়ার পর কোরানের সাংখ্যিক মাহাত্ম্য নিয়ে একটা নিবন্ধ খুলে ফেললাম। এই নিবন্ধই পরবর্তীতে জীবন বদলে দিয়েছিল, কীভাবে, সেটাতেই আসছি।
সচলায়তন ব্লগে অভিজিৎ রায় ‘বিজ্ঞানময় কিতাব’ নামে এক পোস্ট দিয়েছিলেন ২০০৮ সালের মে মাসে। ধর্মসংক্রান্ত অনেক বিষয়েই আমার সংশয় ছিল, ছিল সেই সংশয় মনের এক কোণে ফেলে রেখে স্বাভাবিক জীবন যাপনের চেষ্টাও। ধর্ম পালন না করলেও সমাজের অন্ধকার শিক্ষায় তখনও। মানতাম ইসলাম একমাত্র ধর্ম, মানতাম আল্লাহ বলে আসলেই একজন আছে, মানতাম তিনি বই লিখে সেটা গোপনে একজনের কানেকানে বলে বিশ্বমানবতাকে পথ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু অভিজিৎ রাযের ‘বিজ্ঞানময় কিতাব” লেখাটা পড়ে সেদিন সবকিছু তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়ল। অনুভব করলাম এতোদিন যা জানতাম সব মিথ্যা, যে গ্রন্থকে বিজ্ঞানময় ভাবতাম সেটা মোটেও বিজ্ঞানময় নয়, বিজ্ঞানময়তার উদাহরণগুলো ভক্তদের বানানো মিথ্যা কথা। এভাবে শুধু মিথ্যা বলে একটা গ্রন্থকে এভাবে অলৌকিক করে ফেলা সম্ভব বুঝতে পারলাম। অবশ্য বিজ্ঞানময় কিতাব লেখাতে অভিদা মিরাকল নাইন্টিনের উল্লেখ করেননি। বুঝে গেলাম এটাও মিথ্যা দাবিই হবে। ইন্টারনেটে খুঁজলাম, অভিদার কাছে জানতে চাইলাম এবং দেখলাম আসলেই তাই। সেই থেকে শুরু আমার ধর্ম সংক্রান্ত সংশয়ী চিন্তা। যত গভীরে যেতে থাকলাম, যত পড়তে থাকলাম, তত দেখলাম শৈশব থেকে লালন করা সংস্কারগুলো তাসের ঘরের মতো ভেঙে যাচ্ছে। হাজার বছর ধরে চলা ধর্মীয় ভণ্ডামি আর মিথ্যাচারের মুখোশ ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকল আমার কাছে। শিক্ষানবিস তখন বিজ্ঞান এবং মাঝে মাঝে ধর্ম বিজ্ঞান, সংশয়বাদ নিয়ে লিখত। আমি সেগুলো পড়তাম, আর পড়তাম মুক্তমনার বিশাল আর্কাইভ। নিজেও তখন একটু একটু ব্লগিং শুরু করেছি যদিও সেটা নিতান্ত- ‘ভাত খেতে যাচ্ছি, খেয়ে এসে ঘুমাবো’ টাইপের কথাবার্তা। এভাবেই চলছিল দিন। হঠাৎ একদিন মনে হলো, একটা পাপ মোচন করা দরকার। উইকিতে মিরাকল নাইন্টিন নিবন্ধের পাপ মোচন। চিন্তা পর্যন্তই। এরপর হঠাৎ একদিন ক্যাডেট কলেজ ব্লগে মিরাকল নাইন্টিন নিয়ে পোস্ট আসলো। সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে কোরানের সব কিছুতে আছে মহান উনিশ। আল্লাহর অস্তিত্বের বাস্তব প্রমাণ একেবারে। আমি গা ঝাড়া। দিয়ে বসলাম। মিরাকল নাইন্টিনের ভণ্ডামি তুলে ধরে একটা ব্লগ লিখলাম। এই লেখা যেহেতু আমার পাপমোচন লেখা ছিল তাই এসব বিষয় নিয়ে পুনরায় আর কোনো লেখার আগ্রহ ছিলোনা। কয়েকমাস পরে, অভিদা আমাকে একটা মেইল দিলেন, মেইলের বিষয়বস্তু উনি নেট খুঁজে আমার মিরাকল নাইন্টিন লেখাটা পড়েছেন, আমি যেন মুক্তমনায় নিবন্ধন করে লেখাটা সেখানেও রাখি। আরেকবার মুগ্ধ হবার পালা। কারণ তখন অভিজিৎ রায় এবং বন্যা আহমেদের লেখা বই পড়ে, মুক্তমনার লেখা পড়ে তাদের চিনেছি এবং তারা দুইজনেই ছিলেন আমার কাছে বিশাল উচ্চতার একজন মানুষ। সেই অভিদা আমাকে মেইল করেছেন। তারপরই থেকেই মুক্তমনায় নিবন্ধন করে ধীরে ধীরে সেখানে লেখালেখি শুরু করি মূলত বিবর্তন, জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে।
২০০৯ এর ডিসেম্বরের দিকে অভিদা আর বন্যাপা ঢাকায় এসেছিলেন। অভিজিৎ রায় আগে থেকেই বলেছিলেন আগমনের খবর। উনারা ঢাকা আসা মাত্রই ছুটে গেলাম বন্ধু শিক্ষানবিস সহ। সুটকেস ভর্তি বই এবং চকলেট নিয়ে এসেছিলেন বন্যাপা আর অভিদা। আমরা নিজেদের বই ভাগাভাগি করে, সে বইয়ের গন্ধ শুকতে শুকতে আর চকলেট খেতে খেতে বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ গঠনে তরুণদের ভূমিকা এবং করণীয় নামক বিষয় নিয়ে বিশাল জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করছিলাম। একেবারে শেষ মুহূর্তে অভিদা কোন চিপা থেকে যেন ভিক্টর স্টেংগরের ‘নিউ এইথিজম” বইটা বের করে শিক্ষানবিসের হাতে দিয়ে বললেন- পড়তে। অনেক কিছু জানা যাবে। শিক্ষানবিসের আগে সে বই আমি পড়া শুরু করলাম। ‘অনেক কিছু জানার জন্য” না বরঞ্চ বইয়ের শুরুতে INGERSOLL’S VOW নামে ইঙ্গারসল সাহেবের একটি বক্তৃতার কিয়দংশ পড়ে মুগ্ধ হবার কারণে। অবিশ্বাসের দর্শন নিয়ে তখন আমার অনেক আগ্রহ, যা পাই তাই খাই অবস্থা। বাংলাদেশ থেকে ফিরে গিয়ে প্রায় একবছর পর অভিদা চিঠি দিয়ে বললেন- অবিশ্বাসের দর্শন নিয়ে একটা বই আমরা দুইজন মিলে লিখতে পারি কিনা। অভিদার সাথে লেখালেখির সূচনা হলো আমার। ২০১১ সালে শুদ্ধস্বর থেকে প্রকাশিত হয় ‘অবিশ্বাসের দর্শন। বইটি সম্পাদনা কাকে দিয়ে করানো হবে সেটা ঠিক করতে আমার কিংবা অভিদার এক মুহূর্তও চিন্তা করতে হয় নি। ছিলেন অকালে হারিয়ে ফেলা অনন্ত বিজয় দাশ। অবিশ্বাসের দর্শন’ বইটি সম্পর্কে অনন্ত দা ফ্ল্যাপে লিখেছিলেন,
‘আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বশেষ তত্ব-তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তি করে লেখা অবিশ্বাসের দর্শন বইটি বাংলাভাষী ঈশ্বরবিশ্বাসী থেকে শুরু করে সংশয়বাদী, অজ্ঞেযবাদী, নিরীশ্বরবাদী কিংবা মানবতাবাদী এবং সর্বোপরি বিজ্ঞানমনস্ক সবার মনের খোরাক জাগাবে। ধর্মান্ধতা এবং কুসংস্কার মুক্তির আন্দোলনের মাধ্যমে আগামী দিনের জাত-প্রথা-ধর্ম বর্ণ-শ্রেণিবৈষম্যমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখা মানুষের গণজোয়ারকে এই বই প্রেরণা জোগাবে।
এলাম আমরা কোথা থেকে, কোথায়ই বা যাচ্ছি আমরা, এই অনন্ত মহাবিশ্বের সূচনা হলো কীভাবে, এর শেষই বা কোথায়, এই মহাবিশ্ব তৈরি বা চালানোর পেছনে কি আছেন কোনো অপার্থিব সত্ত্বা, তিনি কি আমাদের প্রার্থনা শোনেন- এ প্রশ্নগুলো শতাব্দী-প্রাচীন চিরচেনা প্রশ্ন। প্রশ্নগুলো নতুন নয়। নানা ধরনের উত্তর সমৃদ্ধ বইও বাংলা ভাষায় কম লেখা হয় নি। তবে এ ধরনের অধিকাংশ প্রচলিত বইয়ে যুক্তির চেয়ে স্থান পেয়েছে অন্ধবিশ্বাস, বিজ্ঞানের বদলে স্থান পেয়েছে কূপমন্ডুকতা। অবিশ্বাসের দর্শন বইটিতে চিরায়ত গড়ালিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে আমরা বরং প্রশ্ন করেছি, পাঠকদেরও অনুরোধ করেছি ‘ক্ষতবিক্ষত হতে প্রশ্নের পাথরে। সেই সাথে নির্মোহভাবে উপস্থাপন করেছিলাম এই অন্তিম প্রশ্নগুলোর রহস্য উন্মোচনে বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক অর্জনগুলো। এই চিরচেনা প্রশ্নগুলোর উত্তর সন্ধানে বিজ্ঞানের অর্জন স্থান পাওয়ায় তা চুয়াডাঙ্গা থেকে সুদূর আইসল্যান্ড প্রবাসী বাংলাভাষী বহু বিজ্ঞানমনস্ক পাঠকের মনে আলোড়ন জাগিয়েছে। বইটি প্রকাশের পর থেকে অসংখ্য মানুষ ফোন, ইমেইল, ব্লগ, ফেসবুক, টুইটারে তাদের মতামত জানিয়েছেন। বিজ্ঞান, মুক্তচিন্তা, সংশয়বাদ এবং যুক্তিবাদ নিয়ে বাংলায় প্রকাশিত যে সমস্ত বই বাজারে আছে, তার মধ্যেও অগ্রগণ্য বই হিসেবে পাঠকেরা অবিশ্বাসের দর্শনকে স্থান দিয়েছেন। ২০১২ সালে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। তারপর দীর্ঘ বিরতি। ২০১৩ সালেই সব কপি শেষ হয়ে গেলো দ্বিতীয় সংস্করণের। ২০১৪ সালে অভিদার সাথে মিলে বইটি আবার ঠিকঠাক করে দেওয়া হলো জাগৃতিকে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের জন্য। ফয়সাল আরেফীন দীপন ভাই বইটা নিষ্ঠার সাথে প্রকাশ করেছিলেন, এবং বিশ্বাসের ভাইরাস ও অবিশ্বাসের দর্শন প্রকাশের মাধ্যমে হয়ে গিয়েছিলেন অপরাধী। বিশ্বাসের ভাইরাসে আক্রান্ত মৌলবাদী জঙ্গীরা তাকে হত্যা করেছিল চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে তার অফিসে ঢুকে।
২০০৯ সালে অভিজিৎ দা ঢাকায় এসে ‘সমকামিতা’ বইটির জন্য বেশ কিছু সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। পরের বছর শুদ্ধস্বর বইটি প্রকাশ করে। সচলায়তনের কল্যাণে টুটুল ভাইযের সাথে আমার আগেই পরিচয় ছিল। অভিদাকেও পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম তার বইগুলো প্রকাশে টুটুল ভাইযের আগ্রহ দেখে। সমকামিতার পরে অবিশ্বাসের দর্শন (২০১১), বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের আলোকে লেখা অভিদার ‘ভালোবাসা কারে ক্য’ ২০১২ সালে প্রকাশিত হয় শুদ্ধস্বর থেকে। সেবার অভিদা ঢাকায় এসেছিলেন লেখক হিসেবে প্রথমবারের মতো বইমেলা পালন করতে, একা। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করি। অভিদা যতদিন ছিলেন, প্রতিদিন দেখা হতো, কথা হতো, বইমেলায় ঘোরাঘুরি, আজ্ঞা, খাওয়াদাওয়া, রাতের বেলা কার্জন হলের পুকুর পাড়ে বিশ্রাম নেওয়া, বাইকে করে অভিদাকে বাসায় পৌঁছে দেওয়া। মনে আছে ২০১২ সালের বইমেলা থেকে অভিজিৎ দা বন্যাপাকে ফোন করে জানিয়েছিলেন- বন্যা তুমি বিশ্বাস করবানা কত মানুষ আমাদের লেখা পড়ে, কতো আগ্রহী মানুষ ঘিরে ধরে রেখেছে আমাকে মেলা জুড়ে, তোমাকে মিস করছি, এরপর আমি বইমেলায় আসলে তোমাকে আমার সাথে আসতেই হবে।
২০১৫ এ বন্যাপাকে সাথে নিয়ে আসবেন বলে গিয়েছিলেন অভিদা। আসলেন তিনি। এবার বইমেলায় তার নতুন দু’টো বই, শুদ্ধস্বর থেকে প্রয়াত গণিত অধ্যাপক মীজান রহমানের সাথে যৌথভাবে লেখা ‘শূন্য থেকে মহাবিশ্ব এবং অবসর থেকে ‘ভিক্টোরিয়া ওকাম্পো’ প্রকাশিত হলো। এরসাথে যুক্ত হলো, অবিশ্বাসের দর্শনের জাগৃতি সংস্করণ এবং বিশ্বাসের ভাইরাসের দ্বিতীয় সংস্করণ। শূন্য থেকে মহাবিশ্ব বইটার সম্পাদনায় জড়িত ছিলাম। বইয়ের সম্পর্কে মন্তব্য জানাতে বলেছিলেন অভিদা। পাঠিয়েছিলাম তাকে। আরও কয়েকজনের মতামতের সাথে আমার মন্তব্যটাও বইয়ে যুক্ত করেছিলেন তিনি–
মীজান রহমান এবং অভিজিৎ রায় লিখিত ‘শূন্য থেকে মহাবিশ্ব বইটি গণিতের শূন্যের মূৰ্ছনার ঘোড়ায় চড়িযে পাঠককে নিয়ে যাবে শূন্য থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে বর্তমানের কালের সেরা বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিকতম ধারনার এক বৈজ্ঞানিক সঙ্গীতানুষ্ঠানে। সৃষ্টির সূচনা ধর্ম এবং বিজ্ঞান দুটি প্রতিষ্ঠানেরই আগ্রহের বিষয় হলেও দুটি প্রতিষ্ঠান থেকে পাওযা উত্তর সম্পূর্ণ আলাদা। আধুনিক বিজ্ঞান থেকে পাওয়া ফলাফল থেকে আমরা আজ বুঝতে পারছি মহা পরাক্রমশালী কোনো সম্বার হাতে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়নি। মহাবিশ্বের উদ্ভব ঘটেছে শূন্য থেকে, সম্পূর্ণ প্রাকৃতিকভাবে। সভ্যতার এ পর্যায়ে এসে বিজ্ঞান তার সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য উন্মোচনে। এই বইটি তাই বাংলাভাষী বিজ্ঞান ও দর্শনে কৌতূহলী পাঠকের অবশ্যপাঠ্য বই।
২০১৪ সালে জাগৃতি প্রকাশনী থেকে বিশ্বাসের ভাইরাস বইটি প্রকাশিত হবার পর থেকেই মৌলবাদী অপশক্তিরা অভিজিৎ রায়কে রুটিন করে হত্যা করার হুমকি দিতে থাকে। প্রতিদিন একজন করে মানুষকে ‘নাস্তিক’ প্রমাণ শেষে তাকে হত্যা করার আহবান জানিয়ে ফারাবী নামক এক বিকৃত মস্তিষ্কের অমানুষ ততদিনে বাংলাদেশের সামাজিক নেটওয়ার্কের পরিচিত মুখ। নিজেকে কখনও নিষিদ্ধ ঘোষিত ‘হিজবুত তাহরির’, কখনও ‘শিবিরের অনুসারী বলে প্রচার করা ফারাবীর ব্লগে আগমন ঘটেছিল মূলত সহব্লগার মেয়েদের বিরক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে। তার প্রথম পোস্টও ছিল অজানা অচেনা মেয়েদের বিয়ে করার অনুরোধ জানিয়ে’। মূলত বিভিন্ন ভুয়া আইডি খুলে ফেসবুক এবং ব্লগে মেয়েদের অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ প্রস্তাব দেওয়াই ছিল তার কাজ। ফেসবুকে আপনারা যারা নিয়মিত, তারা খেয়াল করে দেখবেন, বাংলা ভাষায় ফেসবুকে যে সকল নারী বিদ্বেষী, অশ্লীল, যৌন সুড়সুড়ির পাতা রয়েছে তাদের মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। এরা ইন্টারনেট থেকে নারীদের বিভিন্ন ছবি সংগ্রহ করে সেটা তাদের অনুসারীদের সামনে উপস্থাপন করে এবং একই সঙ্গে আরও একটা বিষয়ে তারা সমান কম্পাঙ্কে পোস্ট করে। কী সেই বিষয়টা? ধর্ম। যেহেতু বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্ম ইসলাম, তাই এই অশ্লীল পাতাগুলোর কাছেও ধর্ম বলতে কেবল ইসলাম। ফারাবী যেন এই মানুষগুলোরই প্রতিনিধি। যার একমাত্র কাজ ছিল নারীদের উত্যক্ত করা এবং ইসলাম ধর্ম নিয়ে পোস্ট দেওয়া। মৌলবাদীদের চাপাতির আঘাতে নিজ বাসার সামনে খুন হওয়া আহমেদ রাজীব হায়দারের জানাজার ইমামকে হত্যা করার হুমকি দিয়ে গ্রেফতার হয় ফারাবী। জামিনে বের হয়ে আসার পর থেকে নিজেকে শোধরানো তো দূরের কথা, উল্টো ব্যাপক উদ্যমে সে ইসলাম ধর্মকে নিজের মতো ব্যাখ্যা করে সন্ত্রাস কায়েমের আহবান জানানো শুরু করে। সিলেট থেকে প্রকাশিত ‘যুক্তি’ পত্রিকার সম্পাদক অনন্ত বিজয় দাশ সিলেটে নিজ বাসার সামনে নিহত হন মান্নান রাহী নামক ফারাবীর এক ঘনিষ্ঠ সহচরের হাতে। এর আগে তিনি ‘ফারাবীর ফাতরামি’ লেখায় এ প্রসঙ্গে বলে গিয়েছিলেন
এরপর ফারাবী আবির্ভূত হয় ইসলামের খেদমতগার হিসেবে। হেফাজতকারী হিসেবে। আমাদের এখানে একটা কথা প্রচলিত আছে, এরশাদ যদি আমাদের গণতান্ত্রিক রাজনীতির রক্ষক হয় তবে এই রাজনীতিকে ধর্ষণ করার জন্য বাহির থেকে কোনো শত্রু আসার প্রয়োজন নেই, তেমন ফারাবীর মতো লুইচ্চা যদি হয়ে যায় ইসলামের খেদমতগার, তবে ইসলামের মুখে চুনকালি মাখাতে কোনো ইসলামবিরোধী, ইসলামবিদ্বেষীর প্রয়োজন নাই।
ইমামকে হত্যার হুমকির অভিযোগে ফারাবীকে আটক করা হলেও সে অস্থায়ী জামিনে জেলহাজত থেকে বের হয়ে আরও বেশি উদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ফেসবুকের অসংখ্য ভুয়া আইডি নিয়ে। আল্লাহ ও রসুলকে তার ভাষায়- যারা অপমান করে, তাদের হত্যা করা জায়েজ। এই ফতোয়া দিয়ে সে একের পর এক শুভবুদ্ধির লেখক, ব্লগার, অনলাইন অ্যাকটিভিস্টদের হত্যার হুমকি প্রদান শুরু করে।
ফারাবীর ভাষ্যমতে–
ইসলাম অর্থ শান্তি নয়, ইসলাম অর্থ হল আত্মসমর্পণ। ইসলামের ভিতরে জিহাদ, কিতাল সবই আছে। আল্লাহ-রসুলকে যারা ঠাণ্ডা মাথায় গালিগালাজ করবে আমরা তাদেরকে হত্যা করব এতে লুকোচুরির কিছু নাই।
২০১৪ সালে বিশ্বাসের ভাইরাস বইটি প্রকাশিত হবার পর থেকেই মৌলবাদী অপশক্তিরা অভিজিৎ রায়কে রুটিন করে হত্যা করার হুমকি দিতে থাকে। উনি দেশের বাইরে থাকেন বিধায়, তাঁর বই বিক্রির দায়ে বাংলাদেশের অনলাইন বই কেনার সাইট ‘রকমারি ডটকম’-এর অফিসের ঠিকানা প্রদান করে পোস্ট দেয় ফারাবী নামক বিকৃত মস্তিষ্কের অমানুষটি। বাংলাদেশে নাস্তিকতা ছড়ানোর অপরাধে সে তার অনুসারীদের রকমারির অফিস আক্রমণের আহ্বান জানায়। একই সঙ্গে স্বত্বাধিকারীর প্রোফাইল উল্লেখ করে তাকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়। এরপর বাংলাদেশের শুভবুদ্ধির সব মানুষকে অবাক করে দিয়ে রকমারির স্বত্বাধিকারী মাহমুদুল হাসান সোহাগ তার স্ট্যাটাসে অভিজিৎ রায়সহ অন্যান্য লেখকদের বিজ্ঞান ও মুক্তচিন্তার বই বিক্রি করার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। কিন্তু তারপরও ফারাবী সন্তুষ্ট না হওয়ায় রকমারি ডটকম তার দেওয়া লিস্ট ধরে নিমেষেই সকল বই তাদের ওয়েবসাইট থেকে প্রত্যাহার করে বিক্রি বন্ধের ঘোষণা দেয়। ব্যক্তিগত সম্পর্ক ধরে এই ঘটনার সময় থেকেই আমি রকমারি ডটকমের সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করি, ফারাবীর ভয়ে ভীত হওয়ার বদলে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে। আমাদের সবার অনুরোধ উপেক্ষা করে ওরা মৌলবাদী তোষণকেই তাদের নীতি হিসেবে গ্রহণ করে এবং নাস্তিকদের বই (পড়ুন। বিজ্ঞান, যুক্তিবাদী এবং প্রগতিশীল বই) বিক্রি চিরতরে বন্ধ করে দেয়। অবশ্য বন্ধ করার আগে নিজেদের মেরুদণ্ডহীনতা ঢাকতে তারা জানিয়ে দেয়, ফারাবীর হুমকির আগে থেকেই তারা এ ধরনের বই সরিয়ে ফেলার উদ্যোগ নিয়েছিল এবং সে উদ্যোগের কারণেই এখন বইগুলো চিরতরে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। অপকর্মের হোতা ফারাবীর বিরুদ্ধে কোনো ধরনের আইনি ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করেনি।
মৌলবাদীদের হত্যার পরোয়ানা সত্ত্বেও প্রিয় বাংলাদেশে এসেছিলেন অভিজিৎ রায়। এসেছিলেন অসুস্থ মা কে দেখতে, অসুস্থ বাবাকে দেখতে, বইমেলায় প্রকাশিত নতুন নতুন বইয়ের গন্ধ শুকতে, বাংলাদেশের বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে। তিনি এসেছিলেন আমাদের অতিথি হয়ে। তিনি জানতেন না, তার প্রিয় বাংলাদেশ বদলে গেছে। ২৩ তারিখ রাতে অভিদাকে মনে করিয়ে দিলাম, হুমকিগুলোকে হালকাভাবে না দেখতে। উনি হেসে উড়িয়ে দিলেন। আমি লেখক মানুষ, আমাকে কেন মারবে?
ফেব্রুয়ারির ছাব্বিশ তারিখ রাত আটটা তেইশ মিনিটে অভিদার কাছ থেকে শেষ এসএমএসটা আসে আমার ফোনে। ‘রায়হান, তুমি কই?’। আমি আর সামিয়া তখন বাসার বাইরে, বইমেলা থেকে অনেক দূরে, বাজার করছি, পরের দিন অভিদা আর বন্যাপা আমাদের বাসায় আসবেন! দেশে আসার পর থেকেই বন্যাপা বলছিলেন, মুক্তমনা ব্লগের যারা দেশে আছে তাদেরকে কোথাও একত্র করতে, তিনি সবাইকে খাওয়াতে চান। আমরা তখন একটা নতুন বাসায় উঠেছি, পাঁচতলার দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেই আধখানা ছাদ, আর আধখানা বাসা। ইচ্ছে ছিল আমরা আট-দশজন মিলে সারাদিন আড্ডাবাজিতে কাটাব, বন্যাপার সাথে মিলে অভিদাকে পঁচাবো, তারপর অভিদার সাথে মিলে বন্যাপাকে, ক্ষুধা পেলে পেট সাঁটিযে অভিদার প্রিয় বিরিয়ানি খাব। ফেব্রুয়ারির চব্বিশ তারিখে আমি আর সামিয়া প্রথম জানতে পারি আমাদের মাতা-পিতা হবার সম্ভাবনার কথা, আমাদের সোফির আগমনের কথা। খবরটা শুনে আমি সামিয়াকে বুকে চেপে ধরে রেখেছিলাম অনেকক্ষণ এবং আমরা দুইজনেই একই সাথে ঠিক করি, বাবা-মা-ভাই-বোনদের পর পরবর্তী পরিবারের সদস্য হিসেবে জানাব বন্যাপা আর অভিদাকে, ফেব্রুয়ারির সাতাশ তারিখে। পাঁচ মাস পেরিয়ে গেলেও ছাব্বিশ তারিখের পরের সেই দিনটা আমার জীবনে আর আসে নি। না ঘটা সেই দিনটা নিয়ে আমি আজও ভাবি, চোখের সামনে নানাভাবে চিত্রায়িত হয় দিনটির প্রতিটি ক্ষণ। ফারাবীতে পরিপূর্ণ এইদেশে আমরা পেয়েছিলাম অভিজিৎ রায়কে, অনন্ত বিজয় দাশ, নীল নীল, ফয়সাল আরেফীন দীপন, রাজীব হায়দারকে। তাঁরা আলো ছড়িয়েছেন, চিন্তার দাসত্ব থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন মানুষকে। অভিজিতের আলোকে গ্রাস করতে অন্ধকার হামলা করেছিল পেছন থেকে। অভিজিতের সেই আলোর মশাল লক্ষ অভিজিতের তুলে ধরতে দেরি হয় নি। এক অভিজিৎ থেকে বাংলাদেশে জন্ম নিচ্ছে লক্ষ অভিজিৎ। অভিজিৎ রাযের বই প্রকাশের জন্য জীবন দিয়েছেন ফয়সাল আরেফীন দীপন, মৌলবাদীদের চাপাতির আক্রমণে প্রায় প্রাণ হারাতে বসেছিলেন শুদ্ধস্বর প্রকাশক আহমেদুর রশীদ টুটুল। জীবন দিয়েছেন বইটির সম্পাদক ‘অনন্ত বিজয় দাশ’। মৌলবাদীরা আমাকেও হত্যা করতে চেয়েছিল, মেডিক্যাল প্রযুক্তিবিদ্যা নিয়ে গবেষণা বন্ধ রেখে, দেশের জন্য কাজ করা বন্ধ রেখে আমাকে দেশ ছেড়ে হতে হয়েছে ‘শরণার্থী’।
আবার আসলো ফেব্রুয়ারি। মহাবিশ্ব সমান শূন্যতা আর বিষাদ নিয়ে। শুদ্ধস্বরের প্রকাশক আহমেদুর রশীদ টুটুল নিজে থেকে ‘অবিশ্বাসের দর্শন’ এর চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এই বই প্রকাশের যে সাহস তিনি দেখিয়েছেন তাতে আসলেই প্রমানিত হয় তাঁর প্রতিষ্ঠিত শুদ্ধস্বর আসলেই ‘মন যোগাতে নয়, মন জাগাতে’ কাজ করে শত বাধা-বিপত্তি-প্রতিকূলতা সত্বেও। বইটির ভেতরের অধ্যায়গুলো অভিজিৎ রায়, অনন্ত বিজয় দাশ, ফয়সাল আরেফীন দীপন যেভাবে রেখে গিয়েছিলেন সেভাবেই রইল। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক প্রকাশকদের মেলা শুরু আগেই হুমকি দিয়ে রেখেছেন। ‘উস্কানিমূলক বই’ প্রকাশ না করতে। জানি না, উনি অবিশ্বাসের দর্শন, বিশ্বাসের ভাইরাস বইগুলোর কথা বুঝিযেছেন নাকি বুঝিয়েছেন হিংসা-বিদ্বেষ-হানানাহিতে পরিপূর্ণ ধর্মগ্রন্থগুলোর কথা। জানি না বলা ঠিক না, আসলে জানি।
ঈঙ্গারসলের সেই প্রতিজ্ঞার কথা আমি ভুলে যাই নি, ভুলে যাননি অভিজিৎ রায়ও। সেই প্রতিজ্ঞা দিয়েই শেষ হোক, অবিশ্বাসের দর্শনের চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকা। আমাদের জীবন দীপান্বিত হোক, মুক্ত হোক বিশ্বাসের ভাইরাস থেকে।
যেদিন নিশ্চিতভাবে বুঝে গেলাম আমার চারপাশের সবকিছুই প্রাকৃতিক, সকল দেবতা, অপদেবতা কিংবা ঈশ্বর মানুষের সৃষ্ট পৌরাণিক চরিত্র ব্যতীত কিছুই নন, সেদিন সত্যিকারের স্বাধীনতার তীব্র আনন্দে মাতোয়ারা হয়েছিল আমার মন, শরীরের প্রতিটি কণা, রক্তবিন্দু, ইন্দ্রিয়। আমাকে সীমাবদ্ধ করে রাখা চার দোল টুকরো টুকরো হয়ে মিশে গেলো ধুলোয়, আলোর স্রোতে আলোকিত হয়ে গেলো আমার অন্ধকূপের প্রতিটি কোণ। সেদিন থেকে আমি কারও চাকর, সেবক বা বান্দা নই। এই পৃথিবীতে আমার কোনো মনিব নেই, আমার কোনো মনিব নেই এই সীমাহীন মহাবিশ্বেও।
আমি স্বাধীন, মুক্ত চিন্তা করতে, চিন্তারাজি প্রকাশে, আদর্শ নির্ধারণে, ভালোবাসার মানুষদের সঙ্গী করে নিজের মতো বাঁচতে। আমি স্বাধীন আমার মানসিক এবং শারীরিক ক্ষমতা ব্যবহারে, প্রতিটি ইন্দ্রিয় দিয়ে কল্পনার ডানা মেলে উড়ে যেতে, নিজের মতো স্বপ্ন দেখতে, আশা করতে। আমি স্বাধীন— নিজের মতো ভাবতে। আমি স্বাধীন নির্দয়, উগ্র ধর্মকে অস্বীকার করতে। আমি স্বাধীন- অসভ্য, মূর্খের ‘অলৌকিক গ্রন্থসমূহ’ এবং এগুলোকে পুঁজি করে ঘটা অসংখ্য নিষ্ঠুরতাকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে। আমি স্বাধীন অসংখ্য মহাজাগতিক মিথ্যা থেকে, স্বাধীন সীমাহীন শাস্তির ভীতি থেকে, আমি স্বাধীন ডানাওয়ালা ফেরেশতা থেকে, শয়তান থেকে, জ্বিন-ভূত এবং ঈশ্বর থেকে। জীবনে প্রথমবারের মতো আমি স্বাধীন। আমার চিন্তার রাজ্যে সেদিন থেকে নেই আর কোনো নিষিদ্ধ জায়গা, নেই কোনো অশরীরী শৃঙ্খল যা বেঁধে রাখে আমার অবয়বকে, আমাকে রক্তাক্ত করার জন্য নেই কোনো অলৌকিক চাবুক, আমার মাংসের জন্য নেই কোনো আগুন। আমার মাঝে নেই ভয, আমার মাঝে নেই অন্যের দেখানো পথে হাঁটার দায়বদ্ধতা, আমার প্রয়োজন নেই কারও সামনে অবনত হওয়া, কাউকে পূজা করা, আমার প্রয়োজন নেই মিথ্যে কথা বলারও। আমি মুক্ত। ভয়-ভীতি, মেরুদণ্ডহীনতা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সেদিন আমি প্রথমবারের মতো উঠে দাঁড়িয়েছিলাম, জগতকে নতুন করে দেখার, ভাবার চেতনা নিয়ে।
আমার অন্তর সেদিন কৃতজ্ঞতায় ভরে গিয়েছিল। আমি কৃতজ্ঞতা বোধ করেছিলাম ইতিহাসের সেই সব নায়কদের প্রতি, মানুষের প্রতি যারা নিজের জীবন বিপন্ন করেছিল, বিসর্জন দিয়েছিল মানুষের হাত এবং মস্তিষ্কের স্বাধীনতা যুদ্ধে। আমি ধন্যবাদ জানিয়েছিলাম পৃথিবীর আলোকিত সকল সন্তানদের, যাদের কেউ আত্মাহুতি দিয়েছিল মূর্খের সাথে যুদ্ধে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিল অন্ধ প্রকোষ্ঠে আবদ্ধাবস্থায়, যাদের মাংস পুড়েছিল ধর্মান্ধদের আগুনে। আলোকিত সেইসব সাহসী মানুষেরা, যারা এসেছিল পৃথিবীর আনাচে-কানাচে, যাদের চিন্তায় কর্মে স্বাধীনতা পেয়েছে মানুষের সন্তানেরা। অতঃপর আমি নীচু হলাম, যে আলোর মশাল তারা জ্বালিয়েছিলেন সে আলোর মশাল তুলে নিলাম নিজের হাতে, উঁচু করে তুলে ধরলাম সেটা, এ আলো নিশ্চয়ই একদিন জ্য করবে সকল অন্ধকার।
রায়হান আবীর
কানাডা
ফেব্রুয়ারি ১, ২০১৬
.
জাগৃতি সংস্করণের ভূমিকা
সিলেট থেকে প্রকাশিত ‘যুক্তি’ পত্রিকার সম্পাদক অনন্ত বিজয়। দশ ‘অবিশ্বাসের দর্শন’ বইটি সম্পর্কে ফ্ল্যাপে লিখেছিলেন, ‘আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বশেষ তত্ব-তথ্য-উপাত্তের উপর ভিত্তি করে লেখা অবিশ্বাসের দর্শন বইটি বাংলাভাষী ঈশ্বরবিশ্বাসী থেকে শুরু করে সংশয়বাদী, অজ্ঞেয়বাদী, নিরীশ্বরবাদী কিংবা মানবতাবাদী এবং সর্বোপরি বিজ্ঞানমনস্ক সবার মনের খোরাক জাগাবে। ধর্মান্ধতা এবং কুসংস্কার মুক্তির আন্দোলনের মাধ্যমে আগামী দিনের জাত-প্রথা-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেনিবৈষম্যমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখা মানুষের গণজোয়ারকে এই বই প্রেরণা জোগাবে। সে প্রত্যাশা কতটা পূরণ হয়েছে আমরা জানিনা, তবে বইটি যে বহু পাঠকের হৃদয়ে একটি স্থায়ী আসন তৈরি করে ফেলেছে সেটি বলাই বাহুল্য। ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং প্রথাগত ধর্ম নিয়ে যৌক্তিক আলোচনা সমৃদ্ধ ‘অবিশ্বাসের দর্শন’ বইটি শুদ্ধস্বর থেকে প্রথমে প্রকাশিত হয় ২০১১ সালের ‘অমর একুশে গ্রন্থমেলা’র প্রথম দিনে। প্রথম সংস্করণের যে কয়টি কপি ছাপা হয় তা ২০১১ সালের মেলার প্রথম দশ দিনেই শেষ হয়ে যায়। বইয়ের চাহিদার কারণে মেলার শেষ দিকে দ্বিতীয় দফায় আবার ‘অবিশ্বাসের দর্শন’ প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বইটির প্রথম সংস্করণের অতিমূল্যের কারণে অনেক পাঠকের কাছে বইটি পৌঁছাতে পারছে না এই বিবেচনায় ২০১২ সালে ‘অবিশ্বাসের দর্শন’ বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় পেপারব্যাকে। মাত্র এক বছরে পেপারব্যাকে ছাপানো সহস্রাধিক কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। ‘অবিশ্বাসের দর্শন’ বইটি বাংলাভাষী শুভ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কাছে পৌঁছুবে এমন একটা সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা লেখকদের মনে ছিলো না-তা নয়, কিন্তু বইটি সাধারণ পাঠকদের মাঝেও যে ভাবে আলোড়ন তৈরি করেছে তা ছিলো সত্যিই অপ্রত্যাশিত। অনেক পাঠক বইটি পড়ে জানিয়েছিলেন, প্রয়াত ড. হুমায়ুন আজাদের ‘আমার অবিশ্বাস’ বইটির পর ঈশ্বর-ধর্ম সংক্রান্ত এতো গভীর আলোচনাসমৃদ্ধ বই বাংলা ভাষায় আর প্রকাশিত হয় নি। অসাধারণ কাব্যিক ভাষায় লেখা ‘আমার অবিশ্বাস’ বইটি এ বইয়ের দু’লেখকেরই প্রিয় বইয়ের তালিকার শীর্ষস্থানে রয়েছে। ‘অবিশ্বাসের দর্শন’ বইটিকে সে বইয়ের সাথে তুলনা আমাদের জন্য বিব্রতকর, কিন্তু সেই সাথে অনেক আনন্দ এবং গর্বেরও।
এলাম আমরা কোথা থেকে, কোথায়ই বা যাচ্ছি আমরা, এই অনন্ত মহাবিশ্বের সূচনা হল কীভাবে, এর শেষই বা কোথায়, এই মহাবিশ্ব তৈরি বা চালানোর পেছনে কী আছেন কোনো অপার্থিব। সত্ত্বা?, তিনি কি আমাদের প্রার্থনা শোনেন- এ প্রশ্নগুলো শতাব্দী প্রাচীন চিরচেনা প্রশ্ন। প্রশ্নগুলো নতুন নয়। নানা ধরণের উত্তর সমৃদ্ধ বইও বাংলা ভাষায় কম লেখা হয় নি। তবে এ ধরণের অধিকাংশ প্রচলিত বইয়ে যুক্তির চেয়ে স্থান পেয়েছে অন্ধবিশ্বাস, বিজ্ঞানের বদলে স্থান পেয়েছে কূপমণ্ডুকতা। অবিশ্বাসের দর্শন বইটিতে আমরা সেই পুরনো ধারা অনুসরণ করিনি। চিরায়ত গড্ডালিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে আমরা বরং প্রশ্ন করেছি, পাঠকদেরও অনুরোধ করেছি ‘ক্ষতবিক্ষত হতে প্রশ্নের পাথরে’। সেই সাথে নির্মোহভাবে উপস্থাপন করেছি এই অন্তিম প্রশ্নগুলোর রহস্য উন্মোচনে বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক অর্জনগুলো। এই চিরচেনা প্রশ্নগুলোর উত্তর সন্ধানে বিজ্ঞানের অর্জন স্থান পাওয়ায় তা চুয়াডাঙ্গা থেকে সুদূর আইসল্যান্ড প্রবাসী বাংলাভাষী বহু বিজ্ঞানমনস্ক পাঠকের মনে আলোড়ন জাগিয়েছে। বইটি প্রকাশের পর থেকে অসংখ্য মানুষ ফোন, ইমেইল, ব্লগ, ফেসবুক, টুইটারে তাদের মতামত জানিয়েছেন। বিজ্ঞান, মুক্তচিন্তা, সংশ্যবাদ এবং যুক্তিবাদ নিয়ে বাংলায় প্রকাশিত যে সমস্ত বই বাজারে আছে, তার মধ্যেও অগ্রগণ্য বই হিসেবে পাঠকেরা অবিশ্বাসের দর্শনকে স্থান দিয়েছেন। কোনো ধরনের প্রচারণা ব্যতীত ফেসবুকে প্রায় পাঁচ হাজার মানুষ বইটিকে পছন্দ করেছেন, অনেকেই রেখেছেন তাদের প্রিয় বইয়ের তালিকায়। এটি নিঃসন্দেহে আমাদের জন্য গর্বের ব্যাপার। ফেসবুক ছাড়াও টুইটার, ব্লগ, বইয়ের ওযেবসাইট গুডরিডস ডট কম সহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যবহার করে পাঠকেরা বইটি সম্পর্কে তাদের মতামত জানিয়েছেন। বাংলা উইকিপিডিয়ার নিবন্ধসহ বেশ অনেক ধরনের নিবন্ধ/ প্রবন্ধে মুক্তমনা লেখকেরা বইটিকে উদ্ধৃত করেছেন। বিগত বছরগুলোতে বইটি নিয়ে বেশ কিছু মূল্যবান আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে দেশের বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এবং ম্যাগাজিনে। যেমন, অবিশ্বাসের দর্শন বইটির একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা স্থান পেয়েছিল সুসাহিত্যিক আহমদ মাযহার সম্পাদিত ‘বইয়ের জগৎ’ পত্রিকার নবম সংখ্যায়। নৃবিদ্যার ছাত্র এবং সাহিত্য সমালোচক শফিউল জয়ের করা সেই শিরোনাম ছিল ‘অবিশ্বাসের দর্শন: যৌক্তিকভাবে মনকে জাগানোর ঐকান্তিক প্রয়াস’[১]। সেই রিভিউটিতে শফিউল জয় ‘অবিশ্বাসের দর্শন’ বইটিকে বাংলা সাহিত্যের জগতে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বই হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন, এবং রিভিউটি সমাপ্ত করেছিলেন এই বলে ‘প্রতিক্রিয়াশীল আর অবৈজ্ঞানিক ধর্মগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অসুস্থভাবে মন জুগিয়ে এসেছে মানুষের, এখন না হয় মন। আমাদের যুক্তির আলোয় জেগে উঠুক’ শফিউল জয়ের এই ঐকান্তিক কামনা যেন আমাদের প্রত্যাশারই নান্দনিক প্রকাশ।
বইটির আরেকটি মূল্যবান রিভিউ করেছেন অস্ট্রেলিয়া প্রবাসী পদার্থবিজ্ঞানী এবং সুলেখক ড. প্রদীপ দেব। মুক্তমনা ব্লগে প্রকাশিত ‘অবিশ্বাসের দর্শন: নবযুগের যুক্তিবাদীর দৃপ্ত পদক্ষেপ’ শিরোনামের এ রিভিউটিতে প্রদীপ দেব যে কথাগুলো উল্লেখ করেছিলেন তা আজও আমাদের জন্য নির্মল আনন্দ এবং অফুরন্ত প্রেরণার নৈমিত্তিক থোরাক”[২]
পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ প্রচলিত ব্যবস্থার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু খুব সামান্য সংখ্যক। কিছু ব্যতিক্রমী মানুষ আছেন যাঁরা পৃথিবীটাকেই বদলে ফেলার চেষ্টা করেন। দিনের পর দিন নিরলস সংগ্রাম চেষ্টা পরিশ্রম অধ্যবসায় দিয়ে পৃথিবীটাকে একটু একটু করে ঠিকই বদলে ফেলেন এই ব্যতিক্রমী মানুষেরা। অথচ তার সুফল ভোগ করেন সবাই যাদের মধ্যে তাঁরাও আছেন যাঁরা ক’দিন আগেও এ পরিবর্তনের ঘোর বিরোধিতা করেছিলেন। ধর্মবাদীদের সাথে মুক্তমনাদের পার্থক্য এখানেই যে ধর্মবাদীরা বড় বেশি বিভাজনপটু। ধর্মবাদীরা তাঁদের নিজস্ব ধর্মের অনুশাসনগুলোর প্রতি কেউ প্রশ্ন তুললেই সেটাকে ব্যক্তিগত শত্রুতার পর্যায়ে নিয়ে যেতেও দ্বিধা করেন না অনেক সময়। বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক যুক্তিতে টিকে থাকতে না পারলে পেশীশক্তি ব্যবহার করেন ধর্মবাদীরা। মধ্যযুগে ধর্মের প্রসার ঘটেছে তলোয়ারের আস্ফালনে, বর্তমানেও ধর্মবাদীদের মূল অস্ত্র আর যাই হোক—যুক্তি নয়। অথচ সারা পৃথিবীতে একজনও যুক্তিবাদী মুক্তমনা পাওয়া যাবে না যিনি যুক্তির বদলে শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করার পক্ষপাতী। যুক্তির শক্তি যে কত প্রবল তা আরো একবার বুঝতে পারলাম অভিজিৎ রায় ও রায়হান আবীরের ‘অবিশ্বাসের দর্শন’ পড়তে পড়তে।
তবে রিভিউটিতে ড.দেব অফুরন্ত প্রশংসাবাক্য প্রক্ষেপণের পাশাপাশি গুটিকয় দুর্বলতারও উল্লেখ করেছিলেন। বিশেষত কিছু লজ্জাজনক বানান এবং মুদ্রণপ্রমাদ গুরুত্বপূর্ণ বইটিকে লঘু করে দিয়েছিল নির্দ্বিধায় বলা যায়। যদিও প্রদীপ দেব রিভিউটি লিখেছিলেন বইটির প্রথম সংস্করণের উপর ভিত্তি করে, এবং তার দেওয়া প্রমাদের তালিকার অধিকাংশই ইতোমধ্যে পরবর্তী সংস্করণে ঠিক করে ফেলা হয়েছিল, তারপরেও কিছু কিছু জায়গায় সমস্যা থেকেই গিয়েছিল। সেগুলোও এবারকার এই নতুন সংস্করণে সংশোধন করে দেয়া গেল। যেমন, ‘বিগব্যাঙ এর জায়গায় ‘বিগব্যাং’ করা হয়েছে, গণিতবিদ ‘ফিবোনাক্কি’র নাম মূল ইতালীয় উচ্চারণ অনুসরণ করে ‘ফিবোনাচি করা হয়েছে। ফিবোনাচি সিরিজে (০, ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১, ৩৪, ৫৫) মাঝখানের একটি সংখ্যা (১) বাদ পড়েছিল। সেটা যোগ করে দেয়া হয়েছে। এ ধরণের ছোটখাটো ভুলভ্রান্তি সংশোধনের পাশাপাশি নতুন নতুন তথ্যের আলোকে পূর্ববর্তী কিছু অনুচ্ছেদ রদবদল করা হয়েছে। বিশেষত লরেন্স ক্রাউসের ‘ইউনিভার্স ফ্রম নাথিং’ গ্রন্থটির প্রকাশ (বাংলাতেও প্রকাশিত হতে চলেছে অভিজিৎ রায় এবং মীজান রহমানের ‘শূন্য থেকে মহাবিশ্ব[৩]), মহাকর্ষীয় তরঙ্গ সনাক্তকরণের সাফল্য প্রভৃতি ঘটনা মহাবিশ্বের উৎপত্তির পেছনে স্ফীতিতত্ত্বের অনুমানকে আরো জোরালো করেছে সাম্প্রতিক সময়গুলোতে। এর পরিপ্রেক্ষিতে চতুর্থ অধ্যায়ের ‘প্রাকৃতিকভাবে কীভাবে মহাবিশ্বের সূচনা হতে পারে’ অংশটি বিবর্ধিত করা হয়েছে।
বইটির বেশ কিছু জায়গায় নতুন তথ্য এবং রেফারেন্স যোগ করা হয়েছে। আমরা আশা করছি,নতুন সন্নিবেশগুলো বইটির মানের উন্নয়ন যেমন ঘটাবে, সেইসাথে সর্বাধুনিক এ তথ্যগুলো পাঠকদের চিন্তার খোরাকও যোগাবে পুরোদমে।
অবিশ্বাসের দর্শনের নতুন এ সংস্করণটি বইটির তৃতীয় সংস্করণ। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ২০১২ সালে প্রকাশিত বইটি পেপারব্যাক সংস্করণের সহস্রাধিক কপি প্রকাশিত হয়েছিল। এক বছরের মাথায় বইটির সকল কপি নিঃশেষ হয়ে যায়। ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্বেও পূর্ববর্তী প্রকাশকের (শুদ্ধস্বর) ব্যর্থতায় বইটি দীর্ঘদিন ধরেই ‘আউট অব প্রিন্ট’। শুধু তাই নয়, একটা সময় পর শুদ্ধস্বরের সত্ত্বাধিকারী আহমেদুর রশীদ টুটুল বইটির পরবর্তী সংস্করণ প্রকাশে অপারগতার কথা জানিয়ে দিলে আমরা নিরুপায় হয়ে বইটি প্রকাশের ভার তুলে দিয়েছি জাগৃতি প্রকাশনীর হাতে প্রকাশনার জগতে জাগৃতি একটি পরিচিত এবং বিশ্বস্ত নামা জাগৃতির সত্বাধিকারী ফয়সল আরেফিন দীপনের হাত দিয়ে ইতোমধ্যেই বের হয়েছে বহুল আলোচিত ‘বিশ্বাসের ভাইরাস’ গ্রন্থটি[৪]। পাঠকপ্রিয় এ গ্রন্থটির জন্য হুমকি ধামকি কম পোহাতে হয়নি লেখক এবং প্রকাশককে রকমারি ডট কম নামে একটি অনলাইন গ্রন্থ-বিপণন প্রতিষ্ঠান তো এক মুখচেনা লুম্পেনের জিহাদি হুমকির মুখে নতি স্বীকার করে বইটিকে তাদের স্টোর হতে সরিযেও নিয়েছেন। এর কিছুটা রেশ ‘অবিশ্বাসের দর্শন’ বইটির উপরেও পড়েছিল। অনেকেই বইটির ভাগ্য নিয়ে ছিলেন চিন্তিত। আমাদের বইয়ের নতুন প্রকাশক অবশ্য সেই সব মৌলবাদী আস্ফালনে ভীত না হয়ে এ ধরণের ‘নাফরমানি’ বই আরো প্রকাশের অঙ্গীকার করেছেন; অবিশ্বাসের দর্শনের পাণ্ডুলিপির জন্য জন্য নিয়মিতভাবে তাগাদা দিয়ে চলেছেন। তার এই নিঃসীম তাগাদার ফসল এই অবিশ্বাসের দর্শনের নতুন সংস্করণ। দীপনের নিষ্ঠা,আগ্রহ,উদ্যম এবং সদিচ্ছা বইটিকে নতুন মাত্রা দেবে বলে আমরা মনে করছি।
মুক্তি আসুক যুক্তির পথ ধরে; আর জীবন হোক দীপান্বিত!
.
প্রথম সংস্করণের ভূমিকা
কীভাবে এলাম আমরা? এই অসীম মহাবিশ্ব, কিংবা সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল, মিঠা নদীর পানি-এগুলোই বা কেমন করে হলো? সবকিছুই কি একজনের ইশারায় একটি নির্দিষ্ট কারণে সৃষ্টি হয়েছে? কৌতূহলী মানুষ সহস্র বছর ধরে সন্ধান করছে এমন সব প্রান্তিক প্রশ্নের উত্তর। ক্ষুদ্র জীবনের সর্বক্ষণ চিন্তিত না থাকলেও প্রশ্নগুলোর কাঁপুনি সামান্য সময়ের জন্য হলেও আমরা সবাই অনুভব করেছি। প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকেই এই প্রশ্নগুলোর উত্তর সন্ধানে নিয়োজিত ছিল প্রথাগত দর্শন। বিজ্ঞান বসে ছিল সাইড লাইনে, সেই ঘোড়দৌড় উপভোগকারী হাজার দর্শকের একজন হিসেবে। কিন্তু এখন দিন পাল্টেছে। প্রান্তিক এই সমস্যাগুলোর অনেকগুলোরই নিখুঁত সমাধান হাজির করতে পারে বিজ্ঞান। গতানুগতিক দর্শন নয় বরং বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের দার্শনিকরাই আজ গহীন আঁধারের উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা। আজকের দিনে কয়েকজন বিখ্যাত দার্শনিকের নাম বলতে বললে হকিং, ওয়াইনবার্গ, ভিক্টর স্টেঙ্গর, ডকিন্স-এদের কথা সবার আগেই চলে আসে। এরা কেউ প্রথাগত দার্শনিক নন, কিন্তু তবুও দর্শনগত বিষযে তাঁদের অভিমত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
সবসময়ই দর্শন আমাদের জ্ঞান চর্চার মধ্যমণি। কিন্তু প্রথাগত দর্শনের স্বর্ণযুগে প্রাকৃতিকবিজ্ঞান ছিল তার সহচরী। এখন দিন বদলেছে-বিশ্বতত্ব, জ্ঞানতত্ব এমনকি অধিবিদ্যার জগতেও প্রাকৃতিকবিজ্ঞান বিশেষ করে পদার্থবিদ্যা শুধু প্রবেশ করে নি, প্রথাগত দর্শনকে প্রায় স্থানচ্যুত করে দিয়েছে। অধিবিদ্যা জানতে হলে তো এখন আর স্পেশাল কোনো জ্ঞান লাগে না। কেবল ধর্মের ইতিহাস, নন্দনতত্ব আর ভাষার মধ্যে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কোনো পথ পায় নি আধুনিক অধিবিদ্যা এবং প্রথাগত দর্শন। অন্যদিকে, আধুনিক পদার্থবিদ্যা আজকে যে জায়গায় পৌঁছেছে সেটি অধিবিদ্যার অনেক প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারে। আমরা আজ জানি, মহাবিশ্বের উৎপত্তি আর পরিণতি নিয়ে একজন প্রথাগত দার্শনিক কিংবা বেদ জানা পণ্ডিত কিংবা কোরআন জানা মৌলবির চেয়ে অনেক শুদ্ধভাবে বক্তব্য রাখতে সক্ষম হবেন একজন হকিং কিংবা ওয়াইনবার্গ। ডিজাইন আর্গুমেন্ট নিয়ে অধিবিদ্যার গবেষকের চেয়ে বিজ্ঞান থেকেই অনেক ভালো দৃষ্টান্ত দিতে পারবেন ডকিন্স বা শন ক্যারল। আজকে সেজন্য মহাবিশ্ব এবং এর দর্শন নিয়ে যেকোনো আলোচনাতে। পদার্থবিজ্ঞানীদেরই আমন্ত্রণ জানানো হয়, অ্যারিস্টটলের ইতিহাস কপচানো কোনো দার্শনিককে কিংবা সনাতন ধর্ম জানা কোনো হেডপণ্ডিতকে নয়। মানুষও বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে নানা রকমের দর্শনের কথা শুনতে চায়, তাদের কথাকেই বেশি গুরুত্ব দেয়। এই বইয়ের মাধ্যমে আমরা বিজ্ঞানের দর্শন এবং চেতনার কথাগুলো বাঙালি পাঠকদের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েছি, যে দর্শন মহাবিশ্ব এবং জীবনের প্রান্তিক সমস্যাগুলোর সমাধানে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে এবং ধর্ম ও প্রথাগত দর্শনকে তার আগের অবস্থান থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে।
আমরা, এ বইয়ের দু’জন লেখকের কেউই প্রথাগত দার্শনিক নই। বরং আমাদের পেশাগত এবং অ্যাকাডেমিক জীবন খুব কঠোরভাবেই বিজ্ঞানের সাথে জড়িত। বিজ্ঞান এবং এর কারিগরি প্রয়োগ নিয়েই আমাদের কাজ কারবার। কাজেই আমরা আমাদের বিজ্ঞানের চোখ দিয়েই প্রান্তিক সমস্যাগুলোকে দেখেছি। পাশাপাশি বহুদিন ধরেই মুক্তমনাসহ বিভিন্ন ব্লগে জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞান, বিবর্তন, মানবতাবাদ, সংশ্যবাদ, যুক্তিবাদসহ বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রান্তিক সমস্যাগুলো নিয়ে লিখছি। বহু গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন এবং সংকলন সাময়িকীতে আমাদের ধ্যানধারণা বিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই বইটি সেসব ধারণারই সুসংবদ্ধ এবং সুগ্রন্থিত প্রতিফলন। আমাদের এই বইটি অবিশ্বাস নিয়ে, এর অন্তর্নিহিত দর্শন নিয়ে। আমরা দু’জনেই প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস মুক্ত এবং ঈশ্বরে অবিশ্বাসী। কেন অবিশ্বাসী, তার বিজ্ঞানভিত্তিক বিশ্লেষণ দেখানোই এ বইয়ের উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, এ বিশ্লেষণ আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত মনগড়া কোনো গল্প নয়, বরং তা হাজির করা হয়েছে একেবারে আধুনিক বিজ্ঞানের জগৎ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন সাম্প্রতিক তথ্যের নিরিখো আমাদের এই গ্রন্থে ঈশ্বর ছাড়াই কীভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে মহাবিশ্বের সূচনা হতে পারে তার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, যা আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক তত্ব এবং পর্যবেক্ষণ দ্বারা খুব জোরালো ভাবে সমর্থিত। এছাড়াও মহাবিশ্বের অস্তিত্বের পেছনে একটি আদি ঐশ্বরিক কারণ খণ্ডন, স্বতঃস্ফূর্তভাবে মহাবিশ্ব উৎপত্তির পেছনে কোনো ধরনের অলৌকিকতার উপস্থিতির অপ্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা ছাড়াও পদার্থের উৎপত্তি এবং শৃঙ্খলার সূচনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রাণের উৎপত্তি থেকে শুরু করে বিবর্তন তত্ব নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে আমাদের বইয়ে। পাঠকেরা এই বইয়ের পথ-পরিক্রমায় জানতে পারবেন, মহাবিশ্ব কিংবা প্রাণ কোনোকিছুর উৎপত্তির ব্যাখ্যাতেই ঈশ্বরকে হাজির করার প্রয়োজন আজ আর পড়ে না। এর পাশাপাশি, আমরা আধুনিক জ্ঞানের নিরিখে সুচারুভাবে খণ্ডন করেছি ‘প্যালের ঘড়ি’ এবং হয়েলের টর্নেডো থেকে বোয়িং’ নামের ছদ্মবৈজ্ঞানিক ধারণাকে। জীবজগতের ডিজাইন এবং ব্যাড-ডিজাইন নিয়েও আলোচনা করেছি নির্মোহ দৃষ্টিকোণ থেকে। শুধু তাই নয়, এই বইয়ে নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের উৎসেরও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করা হয়েছে। আমরা দেখিয়েছি যে, নাকের সামনে ‘স্বর্গের মুলো’ ঝোলাবার কারণে নয়, বরং ডারউইনীয় পদ্ধতিতে প্রাকৃতিকভাবেই পরার্থপরায়ণতা, সহযোগিতা, নৈতিকতা আর মূল্যবোধের মতো অভিব্যক্তিগুলো জীবজগতে উদ্ভূত হতে পারে, যা বিবর্তনের পথ ধরে মানবসমাজে এসে আরও বিবর্ধিত আর বিকশিত হয়েছে। আমরা আশা করি, এ বইটি একজন সচেতন পাঠককে অবিশ্বাস বা নাস্তিকতাই যে একজন বুদ্ধিমান মানুষের সবচেয়ে যৌক্তিক অবস্থান হতে পারে তা বোঝাতে সক্ষম হবে। সে কথা মাথায় রেখেই এ বইয়ের নামকরণ করা হয়েছে ‘অবিশ্বাসের দর্শন’। এই বইটির নাম ‘অবিশ্বাসের দর্শন’ যেমন হয়েছে, তেমনই এ বইয়ের নাম অবলীলায় হতে পারত ‘অবিশ্বাসের বিজ্ঞান’, কিংবা প্রান্তিক বিজ্ঞান’। কারণ আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের চোখ দিয়েই দর্শনের প্রান্তিক সমস্যাগুলোকে দেখেছি, ঠিক যেমন স্টিফেন হকিং তার পদার্থবিজ্ঞানীর চোখ দিয়ে দর্শনের প্রান্তিক সমস্যা আর আমাদের অস্তিত্বের রহস্য নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা করেছেন তার অতি সাম্প্রতিক গ্র্যান্ড ডিজাইন”[৫] বইয়ে, কিংবা জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স করেছেন তার ‘গড ডিলুশন[৬]’ বইয়ে।
বিশ্বাস এবং ধর্ম সবসময়ই একে অন্যের পরিপূরক, আমাদের সমাজে তো বটেই, পাশ্চাত্যেও। আর এ নিয়ে বহু খ্যাতনামা দার্শনিকই চিন্তাভাবনা করেছেন বিভিন্ন সময়ে। স্পিনোজা থেকে ভলতেয়ার, ফুযেরবাক থেকে মার্ক্স পর্যন্ত অনেকেই ভেবেছেন। রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মডেলও তুলে ধরা হয়েছে অনেক। বাংলা ভাষায়ও বেশকিছু বই লেখা হয়েছে। আরজ আলী মাতুব্বর লিখেছেন, লিখেছেন হুমায়ুন আজাদ, লিখেছেন আহমদ শরীফ, লিখেছেন প্রবীর ঘোষ কিংবা ভবানীপ্রসাদ সাহু। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের দার্শনিকেরা বিভিন্নভাবে ধর্মবিশ্বাস এবং সমাজে এর প্রভাবকে বিশ্লেষণ করলেও আমরা মনে করি রিচার্ড ডকিন্সের ‘ভাইরাসেস অব দ্য মাইন্ড’ রচনাটির আগে জৈববৈজ্ঞানিক ভাবে ধর্মের মডেলকে বোঝা যায় নি[৭]। এই প্রবন্ধ থেকে অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যায় যে, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং রীতিনীতিগুলো অনেকটা জু-ভাইরাসের মতোই আমাদের সংক্রমিত করে। সেজন্যই ধর্মের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে মানুষ বহু কিছুই করে ফেলে, যা সুস্থ মস্তিষ্কে কল্পনাও করা যায় না। বিখ্যাত বিজ্ঞানের দার্শনিক ড্যানিয়েল ডেনেট, ডকিন্সের এই ধারণাকেই আরও সম্প্রসারিত করে একটি বই লিখেছেন। সম্প্রতি ব্রেকিং দ্য স্পেল’ শিরোনামে[৮]। একই ভাবধারায় ড্যারেল রে সম্প্রতি লিখেছেন ‘গড ভাইরাস”[৯]। রিচার্ড ব্রডি লিখেছেন ‘ভাইরাস অব দ্য মাইন্ড’[১০] প্রভৃতি। ডকিন্স নিজেও ভাইরাস সংক্রমণের ব্যাপারগুলোকে মিম তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন। সেলফিশ জিন’[১১]এবং সাম্প্রতিক ‘গড ডিলুশন’ বইয়ে তার সেসমস্ত ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে। বাংলাদেশের পাঠকদের জন্য সেসব বই সংগ্রহ অনেকটাই দুরুহ। আমরা আশা করছি, আমাদের এই বইয়ের মাধ্যমে সেসব সাম্প্রতিক ধ্যানধারণাগুলোর সাথে তারা পরিচিত হতে পারবেন। তবে, পাঠকেরা উপলব্ধি করবেন যে, আমরা এই বইয়ে ডকিন্সের ‘মিম’-এর বদলে ‘ভাইরাস’ শব্দটিই অনেক বেশি ব্যবহার করেছি। এর কারণ হচ্ছে, ভাইরাস ব্যাপারটির সাথে সাধারণ পাঠকেরা পরিচিত, মিম’-এর সাথে তেমনটি নয় এখনও। যেকোনো গতানুগতিক ধর্মে বিশ্বাস যে মানুষের মনে একটি ভাইরাস হিসেবেই কাজ করে সেটা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে বিশ্বাসের ভাইরাস’ নামের অধ্যায়ে। আমরা এই বইয়ে উল্লেখ করেছি, মানব মনে প্রোথিত বিশ্বাসগুলো আসলে অনেকটাই ভাইরাস কিংবা প্যারাসাইটের মতো কাজ করে। এদের আক্রমণে মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার বহু উদাহরণ আছে বিজ্ঞানীদের কাছে। যেমন–
.
নেমাটোমর্ফ হ্যেরওয়ার্ম নামে এক ফিতাকৃমি সদৃশ প্যারাসাইট ঘাসফড়িং-এর মস্তিষ্ককে সংক্রমিত করে ফেললে ঘাসফড়িং পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে, যার ফলে নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্মের প্রজননে সুবিধা হয়। অর্থাৎ নিজের প্রজননগত সুবিধা পেতে নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্ম বেচারা ঘাসফড়িঙকে আত্মহত্যায় পরিচালিত করে’[১২]’।
জলাতঙ্ক রোগের সাথে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। পাগলা কুকুর কামড়ালে আর উপযুক্ত চিকিৎসা না পেলে জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু মস্তিষ্ক অধিকার করে ফেলে। ফলে আক্রান্ত মস্তিষ্কের আচরণও পাগলা কুকুরের মতোই হয়ে ওঠে। আক্রান্ত ব্যক্তি অপরকে কামড়াতেও যায়। অর্থাৎ, ভাইরাসের সংক্রমণে মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।
ল্যাংসেট ক্ষুক নামে এক ধরনের প্যারাসাইটের সংক্রমণের ফলে পিঁপড়া কেবল ঘাস বা পাথরের গা বেয়ে উঠানামা করে। কারণ এই প্যারাসাইটগুলো বংশবৃদ্ধি করতে পারে শুধু তখনই যখন কোনো গরু বা ছাগল একে ঘাসের সাথে চিবিযে খেয়ে ফেলে। ফলে প্যারাসাইট নিরাপদে সেই গরুর পেটে গিযে বংশবৃদ্ধি করতে পারে[১৩]।
নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্ম যেমনি ভাবে ঘাসফড়িংকে আত্মহত্যায় পরিচালিত করে, ঠিক তেমনই ধর্মের বিভিন্ন বাণী এবং জিহাদি শিক্ষা মানুষকে অনেক সময়ই ভাইরাস কিংবা প্যারাসাইটের মতো সংক্রমিত করে আত্মঘাতী করে তোলে। ফলে আক্রান্ত সন্ত্রাসী মনন বিমান নিয়ে আছড়ে পড়ে টুইন টাওয়ারের ওপর, কখনোবা সিনেমা হলে, কখনোবা রমনার বটমূলে। নাইন ইলেভেনের বিমান হামলায় উনিশ জন ভাইরাস আক্রান্ত মনন ‘ঈশ্বরের কাজ করছি’-এই প্যারাসাইটিক ধারণা মাথায় নিয়ে হত্যা করেছিল প্রায় তিন হাজার সাধারণ মানুষকে। ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগোর অধ্যাপক ব্রুস লিংকন, তার বই ‘হলি টেররস : থিংকিং অ্যাবাউট রিলিজিয়ন আফটার সেপ্টেম্বর ইলেভেন’ বইয়ে বিষয়টির ওপর আলোকপাত করে বলেন, ‘ধর্মই, মুহাম্মদ আতাসহ আঠারজনকে প্ররোচিত করেছিল এই বলে যে, সংগঠিত বিশাল হত্যাযজ্ঞ শুধু তাদের কর্তব্য নয়, বরং স্বর্গ থেকে আগত পবিত্র দায়িত্ব’[১৪]। হিন্দু মৌলবাদীরাও একসময় ভারতে রাম জন্মভূমি অতিকথনের ভাইরাস বুকে লালন করে। ধ্বংস করেছে শতাব্দী প্রাচীন বাবরি মসজিদ। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মীয় অপবিশ্বাসের অপকারিতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে ‘ধর্মীয় নৈতিকতা, এবং এর পরবর্তী ‘বিশ্বাসের ভাইরাস’ অধ্যায়টিতে। আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই, পৃথিবীতে শান্তি আনার পরিবর্তে অশান্তি সৃষ্টিতেই যুগযুগ ধরে অবদান রেখেছে ধর্মগুলো, হয়ে উঠেছে বিভেদের হাতিয়ার। এই বইয়ে বহু পরিসংখ্যান হাজির করে দেখানো। হয়েছে যে, ধর্ম নৈতিকতার একমাত্র উৎস নয়, কিংবা নাস্তিক হলেই কেউ খারাপ হয় না, যদিও আমাদের সমাজে এটাই ঢালাওভাবে ভেবে নেওয়া হয় আর শেখানোর চেষ্টা করা হয়। আমরা বিভিন্ন দেশের জেলখানার দাগী আসামীদের পরিসংখ্যান উপস্থাপন করে দেখিয়েছি যে, তাদের প্রায় সবাই ঈশ্বরে বিশ্বাসী-আস্তিক। ঈশ্বরে বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস, বেহেস্তের লোভ বা দোজখের ভয় কোনটাই কিন্তু অপরাধীদের অপরাধ থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারে নি। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অবস্থাই এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ আল্লাহর গোনাহ কিংবা ঈশ্বরের ভয়েই যদি মানুষ পাপ থেকে, দুর্নীতি থেকে মুক্ত হতে পারত, তবে তো বাংলাদেশ এতদিনে বেহেস্তে পরিণত হতো। বাংলাদেশে অধিকাংশ লোকই আল্লাহ-খোদা আর পরকালে বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও দুর্নীতিতে এই দেশটি পৃথিবীতে শীর্ষস্থানীয়। ধর্মে বিশ্বাস কিন্তু দেশবাসীকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে পারে নি। এ বইয়ে ব্যক্তিবিশেষের পরিসংখ্যান যেমন দেওয়া হয়েছে, ঠিক তেমনই পাশ্চাত্য বিশ্বে সুইডেন বা ডেনমার্কের মতো প্রায় ধর্মহীন’ দেশগুলোর সমাজব্যবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে ধর্মহীন হওয়া সত্বেও সেসব দেশে পৃথিবীর অন্য অনেক জায়গার চেয়ে অপরাধ প্রবণতা কম এবং সেখানকার নাগরিকেরা অনেক সুখী জীবনযাপন করছে। বিভিন্ন দেশের সামাজিক পরিসংখ্যান উপস্থাপনের পাশাপাশি এ বইয়ে সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার সঠিক ব্যাখ্যা হাজির করা হয়েছে; ধর্মনিরপেক্ষতা মানে কখনোই সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা নয়, বরং এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে একটি মতবাদ, যা মনে করে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি থেকে ধর্মকে পৃথক রাখা উচিত। এধরনের অনেক গভীর রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং দার্শনিক আলোচনা বইটিতে স্থান পেয়েছে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে। কাজেই আগেকার বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ধারা থেকে আমাদের বইটি অনেক দিক থেকেই স্বতন্ত্র, সম্পূর্ণ নতুন একটি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে আমরা বিশ্বাস এবং ধর্ম নিয়ে আলোচনার সুত্রপাত ঘটিযেছি বাঙালি পাঠকদের জন্য। আমরা মনে করি, এই আঙ্গিকে ঈশ্বর ও ধর্মালোচনা বাংলা ভাষায় এই প্রথম।
ঈশ্বরে বিশ্বাস নিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলাদাভাবে আলোচনা করা হয়েছে এই বইয়ে। ঈশ্বরে বিশ্বাস করাটা এক ধরনের কুসংস্কার এবং আমাদের মতে সবচেয়ে। বড় কুসংস্কার। আর সে অপবিশ্বাসকে পুঁজি করে মানুষের আবিষ্কৃত ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থগুলোও অযৌক্তিক মতবাদে পরিপূর্ণ। অন্য সকল ধরনের কুসংস্কার, অপবিশ্বাস, অযুক্তি বধ করতে যেমন আমরা বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হই বিনা দ্বিধায়, তেমনই ঈশ্বর এবং ধর্মালোচনাতেও আমাদের অস্ত্র হতে পারে বিজ্ঞান। বিবর্তন তত্ব থেকে শুরু করে আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ইতোমধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলেছে। যদিও অনেকেই ঢালাওভাবে বলে থাকেন, ‘ঈশ্বর সংজ্ঞায়িত নন’, কিংবা ‘বিজ্ঞান দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব কিংবা অনস্তিত্ব কোনটাই প্রমাণ করা যায় না, কিংবা বলেন ‘ঈশ্বরের অনুপস্থিতি প্রমাণ করা গেলেও সেটা তার অনস্তিত্বের প্রমাণ হতে পারে না’ ইত্যাদি। এই বইয়ে আমরা দেখাব স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নেওয়া এই ধরনের প্রতিটি অনুকল্পই ভুল। আব্রাহামিক ধর্মের ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যগুলোর অনেক কিছুই খুব ভালোভাবে সংজ্ঞায়িত। এ বইয়ে বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে তার অনেক বৈশিষ্ট্যই আধুনিক বিজ্ঞানের চোখে ভ্রান্ত কিংবা যুক্তির কষ্টিপাথরে পরস্পরবিরোধী। তাছাড়া, আধুনিক বিজ্ঞান এখন যে জায়গায় পৌঁছে গেছে ঈশ্বর বলে কিছু থেকে থাকলে কোনো না কোনোভাবে বিজ্ঞানের চোখে তা ধরা পড়ার কথা ছিল। যেসব ক্ষেত্রে ঈশ্বরের উপস্থিত থাকার কথা এতদিন আমরা শুনে এসেছি, সেখানে তার অনুপস্থিতি অবশ্যই তার অনস্তিত্বের উপযুক্ত প্রমাণ আমাদের কাছে। বিবর্তন তত্ব রঙ্গমঞ্চে আসার আগ পর্যন্ত সকল ধর্মগ্রন্থের কল্যাণে আমরা জানতাম ঈশ্বর আদম-হাওয়ার মাধ্যমে মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন। ধর্মগ্রন্থের আয়াতসমূহে আল্লাহ বলেছেন, তিনি আমাদেরকে এক আদি মানুষ আদম হতে সৃষ্টি করেছেন, এবং বিবি হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন আদমের হাড থেকে’[১৫]। আর অন্যদিকে বিবর্তন। বলছে আদি এককোষী জীবের লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তিত রূপ বর্তমান মানুষ। বিবর্তন তত্ত্ব বহু আগেই প্রমাণ করেছে, খ্রিস্টান পাদ্রি জেমস আশারের ৪০০৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ঈশ্বরের বিশ্বসৃষ্টির বাইবেলীয় গণনা কিংবা ২৩৪৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নুহের প্লাবনের কোনো ধরনের বৈজ্ঞানিক সত্যতা নেই। বিজ্ঞানীদের নব নব আবিষ্কারের ফলে মানুষ ধীরে ধীরে বুঝতে পারছে, এই মহাবিশ্ব এবং এই পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভবের পেছনে আসলে কোনো ডিজাইন নেই, পরিকল্পনা নেই, নেই কোনো বুদ্ধিদীপ্ত সত্বর সুমহান উদ্দেশ্য। মহাবিশ্বের উদ্ভব এবং প্রাণের উৎপত্তির পেছনে মুস্থিত প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা এখন আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যেই দেওয়া সম্ভব, যা পরীক্ষালব্ধ উপাত্তের সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ। এছাড়া প্রার্থনায় সাড়া দেওয়ার পরীক্ষাসহ বহু পরীক্ষায় ঈশ্বরের উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়ার কথা থাকলেও সে ধরনের কিছু কথনও পাওয়া যায় নি। ঈশ্বর আজ আধুনিক বিজ্ঞানের চোখে একটি ‘ব্যর্থ অনুকল্প। আমাদের চারপাশের জগতে অতিপ্রাকৃত কোনোকিছুর অস্তিত্ব নেই। একটা সময় প্রাণের অস্তিত্ব ব্যাখ্যার জন্য আর শরণাপন্ন হতে হয়েছিল মানুষকে। আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে ঈশ্বরের মতো আত্মাও একটি বাতিল অনুকল্প। বইয়ের একটি পূর্ণাঙ্গ অধ্যায়ে বিষয়টি নিয়ে বিশদ আলোচনায় বলা হয়েছে, মানুষের অনুভূতি, জন্ম-মৃত্যু থেকে শুরু করে জগতের সবকিছুই প্রাকৃতিক নিয়ম দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, আত্মার মতো অতিপ্রাকৃত কোনোকিছু আমদানির দরকার নেই।
ঈশ্বর অনুকল্পের পাশাপাশি এসেছে ধর্মগ্রন্থে আধুনিক বিজ্ঞান খুঁজে পাওয়ার বিষয়টিও। শতাব্দী-প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলোর বিভিন্ন আয়াত বা শ্লোকের বিভিন্ন চতুর অপব্যাখ্যার মাধ্যমে ইদানীং এর ভেতর আধুনিক বিজ্ঞান খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং মানুষজনকে ভুল বোঝানো হচ্ছে। মরিস বুকাইলি থেকে শুরু করে হারুন ইয়াহিয়া, জাকির নায়েক এবং বাংলাদেশের বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ শমশের আলীসহ আধুনিক বিরিঞ্চি-বাবাদের বিভিন্ন অপব্যাখ্যার জবাব দেওয়া হয়েছে বইয়ের ‘বিজ্ঞানময় কিতাব’ অধ্যায়ে। একই অধ্যায়ে রাশাদ খলিফা বর্ণিত কোরআনের তথাকথিত উনিশ তত্ত্বের নির্মোহ বিশ্লেষণ সংযুক্ত হয়েছে। আমরা দেখিয়েছি কীভাবে রাশাদ খলিফা কোরআনের আয়াতে ইচ্ছেমতো নিজস্ব সংযোজন বিযোজনের মাধ্যমে অর্থাৎ কোরআন টেম্পারিং করে নিউমেরোলজি বা সংখ্যাতত্ব নামক অপবিজ্ঞানের সাহায্যে কোরআনকে অলৌকিক গ্রন্থ বানাতে চেয়েছেন।
বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা নতুন কোনো ঘটনা নয়, এটি চলছে হাজার বছর ধরে। কিন্তু বিজ্ঞানের উপকার গ্রহণে আমরা যতটা না আগ্রহী তার চেয়ে বেশি আগ্রহী বিজ্ঞানের চেতনা পরিহারে। কিন্তু আমরা, নতুন দিনের নাস্তিকেরা উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া অযৌক্তিক বিশ্বাসকে সামান্যতম শ্রদ্ধা দেখাতে রাজি নই। আমরা মনে করি, ধর্মীয় বিশ্বাস আসলে অপবিশ্বাস, যা সমাজের শান্তি বিনষ্টকারী এবং সেইসাথে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা রোধের প্রধানতম অন্তরায় ছাড়া আর কিছু নয়। ছোটবেলার মগজধোলাইয়ের কারণে সমাজের বেশিরভাগ। মানুষই মনে করে থাকেন, জীবনে শান্তি, পবিত্রতা এবং আনন্দ বজায় রাখার জন্য ধর্ম জরুরি। তাদের এই অনুভূতি আমরা কেড়ে নিতে চাই না, তবে আমরা দেখাতে চাই, ধর্ম বিশ্বাস ছাড়াও জীবন একই রকম কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে তার চেয়েও বেশি নৈতিক,আনন্দ এবং পরিপূর্ণতায় ভরা হতে পারে। অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্সের উক্তি দিয়েই বলি-You can be an atheist who is happy, balanced, moral and intellectually fulfilled.’ এ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে বইটির শেষ তিনটি অধ্যায়ে।
২০০৪ সালে স্যাম হ্যারিসের লেখা ‘বিশ্বাসের সমাপ্তি বইটির মাধ্যমে পাশ্চাত্যে সূচনা হয় নতুন এক আন্দোলনের[১৬]। পরবর্তীকালে রিচার্ড ডকিন্স, ভিক্টর স্টেঙ্গর, ড্যানিয়েল সি ড্যানেট এবং ক্রিস্টোফার হিচেন্সের মতো খ্যাতনামা বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকেরা আরও ছয়টি দুনিয়া কাঁপানো বইয়ের মাধ্যমে সমাজ থেকে ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করার জন্য শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেন। উল্লিখিত নাস্তিকদের প্রতিটি বই আমেরিকায় বেস্ট সেলার হয়েছে, যা কিছুদিন আগেও ছিল অকল্পনীয়। এই আন্দোলন পাশ্চাত্যে পরিচিত হয়েছে নতুন দিনের নাস্তিকতা (নব্য নাস্তিকতা New Atheism) হিসেবে। বাংলায় এখনও সে ধরনের কোনো আন্দোলন চোখে পড়ে নি, যদিও আমরা প্রায়ই নিজেদের প্রবোধ দিতে উচ্চারণ করি যে, আমাদের সংস্কৃতিতে বস্তুবাদিতার উপাদান অনেক প্রাচীন। আধুনিক বিজ্ঞানের আলোকে নতুন দিনের নাস্তিকতা আন্দোলনে নিজেদের সম্পৃক্ত করার জন্যই আমাদের এই বই। সকল ধরনের অপবিশ্বাস থেকে সমাজকে মুক্ত করাই এই আন্দোলনের লক্ষ্য। আশা করি, এই বইয়ের মাধ্যমে আমরা দেখাতে পারব যে, নতুন দিনের নাস্তিকতাই একজন বুদ্ধিমান মানুষের জন্য আজ অবশ্যম্ভাবী ও শক্তিশালী একটি যৌক্তিক অবস্থান। আমরা আরও আশা করি বাংলাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী, সংশয়বাদী এবং মানবতাবাদীরা এই আন্দোলনে শরীক হওয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে কুসংস্কার দূরীকরণে এগিয়ে আসবেন। সেটা কেবল একটি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গঠনেই আমাদের সাহায্য করবে না, সাহায্য করবে কট্টর ধর্মীয় মৌলবাদীদের হাত থেকে আমাদের সমাজকে রক্ষা করতে। রক্ষা করবে, ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠা প্রতিক্রিয়াশীল মহলের স্বাধীন বাংলাদেশকে আরেকটি ছোট পাকিস্তান কিংবা তালিবানি আফগানিস্তান বানানোর অপচেষ্টা থেকেও।
আমাদের জীবন দীপান্বিত হোক!
অভিজিৎ রায়।
রায়হান আবীর (raihan1079@gmail.com)
ফেব্রুয়ারি, ২০১১
০১. বিজ্ঞানের গান
নাস্তিক্যবাদ ধর্ম হলে ‘বাগান না করাও একটি শখ, ক্রিকেট না খেলাও একটি ক্রীড়া, কোকেন সেবন না করাও একটি নেশা’। –জুবায়ের অর্ণব[১৭]
মহাবিশ্বের উৎপত্তি আর বিকাশ নিয়ে ২০০৫ সালে অভিজিৎ রায় (এই বইয়ের সহলেখক) লিখেছিলেন, ‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’ শিরোনামের বই[১৮]। বইটির লেখকের কথা’ অংশে বিজ্ঞান সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন–
বিজ্ঞানের অবদান কি কেবল বড় বড় যন্ত্রপাতি বানিয়ে মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য বয়ে আনা? আমাদের স্কুল কলেজে যেভাবে বিজ্ঞান পড়ানো হয় তাতে এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক। ব্যাপারটা আসলে তা নয়। বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে মানুষ বড় বড় যন্ত্রপাতি বানায় বটে; তবে সেগুলো স্রেফ প্রযুক্তিবিদ্যা আর প্রকৌশলবিদ্যার আওতাধীন। বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের অভিযোজন মাত্র। আসলে বিজ্ঞানের একটি মহান কাজ হচ্ছে প্রকৃতিকে বোঝা, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যা খুঁজে বের করা। বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য এখানেই। হ্যাঁ, জ্যোৎস্না রাত কিংবা পাখির কূজনের মতো বিজ্ঞানেরও একটি নান্দনিক সৌন্দর্য আছে, সৌকর্য আছে যার রসাস্বাদন কেবল বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানমনস্ক সর্বোপরি বিজ্ঞানপ্রেমী ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ কার্ল স্যাগান তার বিখ্যাত ‘The Demon-Haunted World’ বইয়ের ভূমিকায় এ কারণেই হয়ত বলেছিলেন, সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলো সঠিকভাবে ব্যাখ্যা না করাকে এক ধরনের বিকৃত মনোভাব বলেই আমার মনে হয়। যখন মানুষ প্রেমে পড়ে, তখন সারা পৃথিবীর কাছে সে তার প্রেমের কথা প্রচার করতে চায়। এ বইটি আমার প্রেমের একটি ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তি, বিজ্ঞানের সাথে আমার সারা জীবনের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ইতিকথা।
প্রাসঙ্গিক কারণে, ঠিক পাঁচ বছর পরের নতুন এই বইয়ে পুরনো কথাগুলোই উঠে এলো আবার। নিঃসন্দেহে এই বইটিও আমাদের প্রেমের একটি ব্যক্তিগত স্বীকারোক্তি হয়ে উঠবে, হয়ে উঠবে বিজ্ঞানের সাথে আমাদের সারা জীবনের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ইতিকথাই।
‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’ বইটি বেরুনোর পরে অনেকেই একে বাংলাদেশে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসারের একটি মাইলফলক হিসেবে দেখেছিলেন। এক বছরেই বইটির প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। ড. শাব্বির আহমেদ, ড. বিপ্লব পাল, ড. হিরন্ময় সেনগুপ্ত, ড. শহিদুল ইসলাম, ড. বিনয় মজুমদারের মতো বরেণ্য লেখক এবং শিক্ষাবিদেরা বইটির রিভিউ করেছিলেন। সেসব রিভিউ প্রকাশিত হয়েছে এনএফবি, অবজারভার, হলিডে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট, ডেইলি স্টার, মৃদুভাষণ, ভোরের কাগজসহ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়।
কিন্তু যে ব্যাপারটি বলার জন্য এখানে এত আয়োজন তা হলো, ‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’ বইটিতে পদার্থবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক ধ্যান ধারণাগুলোর পাশাপাশি, শেষ অধ্যায়টিতে আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বশেষ তত্ব ও তথ্যের আলোকে ঈশ্বর অনুকল্পটি নিয়েও নিরপেক্ষ আলোচনা ছিল। আর এখানেই দেখা দিয়েছিল একটি মজার সমস্যা। ‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’ বইটির ভূমিকা লিখেছিলেন বাংলাদেশের স্বনামখ্যাত পদার্থবিদ অধ্যাপক এ এম হারুন অর রশীদ। তিনি বইটি নিয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাক্য প্রক্ষেপণের পরেও ভূমিকার শেষ দিকে একটি বাক্য জুড়ে দেন–
ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব বিজ্ঞানের বিষয় নয় এটা বুঝতে তরুণ মনের সময় লাগে অনেক, তবে সে পথে আলো হাতে চলা আঁধারের যাত্রীকে নিরুৎসাহিত করা মোটেও উচিত নয় বলেই আমার মনে হয়।
এ এম হারুন অর রশীদ’ ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব বিজ্ঞানের বিষয় নয়’ বলে যে উক্তিটি বইয়ের ভূমিকায় করেছিলেন তা খুব পরিচিত এবং জনপ্রিয় ধারণার প্রতিফলন। এ এম হারুন অর রশীদ থেকে শুরু করে জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখকেরা প্রায়ই আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, বিজ্ঞানের কাজ হচ্ছে পার্থিব জ্ঞানের চর্চা করা, ঈশ্বর কিংবা এধরনের অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে কখনোই কোনো অভিমত দিতে পারে না বিজ্ঞান। তাই এ নিয়ে টু-শব্দ করা বিজ্ঞান লেখকদের অনুচিত। কিন্তু সত্যিই কি তাই?
.
বিজ্ঞান কি অতিপ্রাকৃত বিষয় নিয়ে অভিমত দিতে অক্ষম?
আগের দিনে মানুষেরা বাড়ি থেকে একটু দূরে থাকা পুকুর পাড়ে রাতের অন্ধকারে হঠাৎ আগুন জ্বলতে দেখে ভাবতো সেটা বুঝি কোনো ভূত-জ্বিন-পরীর কাজ। এরপর মঞ্চে হাজির হলো বিজ্ঞান বিজ্ঞান এসে আমাদের জানাল মিথেন গ্যাসের কথা। আমাদের মনে থাকা জ্বিন পরীর গল্পকে শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে সেখানে বসিয়ে দিল আসল সত্য। এখন আর কেউ পুকুর পাড়ে আগুন জ্বলতে দেখলে ভয় পায় না, তারা জানে এটা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ব্যাপার।
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়-এভাবেই মানুষের মনে জমে থাকা অসংখ্য কুসংস্কারের কালো নিকষ আঁধার দূর করে আশার প্রদীপ জ্বালিয়েছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের এই গুণের কারণে এই ধারণাটিকে আমরা আশীর্বাদ মনে করি। কিন্তু যেই বিজ্ঞান আমাদের মনের সবচেয়ে বড় কুসংস্কার সম্পর্কে কিছু বলতে যায়, অমনি শুরু হয়ে যায় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য। আমাদের মনের কুসংস্কারটিকে সমূলে উৎপাটিত করে দিবে বিজ্ঞান, আমাদের মৃত্যু পরবর্তী সুখের জীবনকে তছনছ করে দিবে বিজ্ঞান, অবচেতন মনের এই ভাবনায় আমরা কখনোই বিজ্ঞানের সেই কুসংস্কার নিয়ে কথা বলা মেনে নিতে পারি না।
ইন্টারনেটে ধর্ম ও বিজ্ঞান নিয়ে লিখতে গিয়ে আমরা প্রায়শই এমন মানুষের মুখোমুখি হই। তাদের মাঝে অনেকেই বলেন, বিজ্ঞান হলো যুক্তি এবং কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োগ আর ধর্ম হলো বিশ্বাস। এ দুয়ের অবস্থান সম্পূর্ণ আলাদা বলয়ে। বিজ্ঞান দিয়ে কোনোভাবেই ঈশ্বর নামক বিষয়ে কথা বলা যাবে না। তারা বিজ্ঞান ভালোবাসেন কিন্তু একই সাথে মনে করেন যে, ঈশ্বরের অনস্তিত্ব প্রমাণে বিজ্ঞানকে টেনে আনাটা খুবই হাস্যকর। যদিও তারা ভূতে বিশ্বাসের মতো বিষয়ে বিজ্ঞানকে টেনে নিয়ে এসে সেই বিশ্বাসকে কচুকাটা করাটাকে হাস্যকর মনে করেন না, কোনোভাবেই হাস্যকর মনে করেন না অসুখ বিসুথে কিংবা সাপে কামড়ালে সাপের মন্ত্র না জপে ডাক্তারের শরণাপন্ন হওয়াকে, তারা শুধু হা রে রে করে ওঠেন যখন ধর্ম, ঈশ্বর আর অতিপ্রাকৃত বিষয়ে কথা বলার চেষ্টা করা হয়।
কিন্তু সৌভাগ্যের ব্যাপার হলো, পশ্চিমা বিশ্বের প্রথিতযশা বিজ্ঞানীরা আজ ‘ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা অনস্তিত্ব বিজ্ঞানের বিষয় নয়’ ধরনের গড্ডালিকা প্রবাহে গা না ভাসিয়ে না দিয়ে সঠিক অবস্থান নিতে শুরু করেছেন। যেমন, বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তার অতি সাম্প্রতিক বই ‘গ্র্যান্ড ডিজাইন’-এ সরাসরি বলেছেন[১৯]– মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে ঈশ্বরের কোনো ভূমিকা নেই। মহাবিশ্ব পদার্থবিজ্ঞানের নিয়মনীতি অনুসরণ করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৈরি হয়েছে। মহাবিশ্বের উৎপত্তি এবং অস্তিত্বের ব্যাখ্যায় ঈশ্বরের আমদানি একেবারেই অযথা। তার নতুন বই ‘গ্র্যান্ড ডিজাইন’-এ খুব সুস্পষ্টভাবেই বলেন (গ্র্যান্ড ডিজাইন, পৃষ্ঠা ১৮০)–
মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সূত্রের মতো পদার্থবিজ্ঞানের বিভিন্ন সূত্র কার্যকর রয়েছে, তাই একদম শূন্যতা থেকেও মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্ভব এবং সেটি অবশ্যম্ভাবী। ‘স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎপত্তি হওয়ার কারণেই ‘দ্যের ইজ সামথিং, র্যাদার দ্যান নাথিং’, সে কারণেই মহাবিশ্বের অস্তিত্ব রয়েছে, অস্তিত্ব রয়েছে আমাদের। মহাবিশ্ব উৎপত্তির সময় বাতি জ্বালানোর জন্য ঈশ্বরের কোনো প্রয়োজন নেই।
আসলে ঈশ্বরসহ বেশ কিছু তথাকথিত অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপারে আধুনিক বিজ্ঞান যে সুস্পষ্ট অভিমত দিতে পারে তা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে খুব ভালো করে বোঝা যাচ্ছিল। বিশেষত ২০০৪ সাল থেকে ২০০৮ সালের মধ্যে পশ্চিমা বিশ্বে পাঁচজন বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকদের ছয়টি ‘বেস্ট সেলিং’ বই প্রকাশিত হয়। সেই স্বনামখ্যাত লেখকেরা হচ্ছেন-স্যাম হ্যারিস, ড্যানিয়েল ডেনেট, রিচার্ড ডকিন্স, ভিক্টর স্টেঙ্গর এবং প্রয়াত ক্রিস্টোফার হিচেন্স। তাঁরা খুব সুস্পষ্টভাবে অভিমত দিয়েছেন যে, আধুনিক বিজ্ঞান আজ যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, সে অবস্থান থেকে সে ঈশ্বর সংক্রান্ত বিভিন্ন অনুকল্পগুলো পরীক্ষা করে উপসংহারে পৌঁছুতে সক্ষম। তাঁদের এই নতুন আন্দোলনকে বিশ্বব্যাপী ‘নব্য নাস্তিকতা’র আন্দোলন (New Atheism Movement) হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে।[২০]
বিগত কয়েক দশকে বিজ্ঞান এবং দর্শনশাস্ত্রের নানা দিকে বিবর্তন ঘটেছে। ঈশ্বর সংজ্ঞায়িত নন, ঈশ্বর বিজ্ঞানের বিষয় নন, কিংবা ঈশ্বরকে প্রমাণ বা অপ্রমাণ কোনোটাই করা যায় না–এমন বক্তব্যগুলোকে এখন আর ঢালাওভাবে পতাকার মতো বহন করা হয় না। জুডিও খ্রিস্টান-ইসলামিক ঈশ্বরের অনেক সুসংজ্ঞায়িত বৈশিষ্ট্য ধর্মগ্রন্থ থেকে জানা যায়। যেমন, সেই ঈশ্বর একজন ব্যক্তি ঈশ্বর-তিনি রাগ, ক্ষোভ, ঘৃণা প্রকাশ করেন, অবিশ্বাসীদের শাস্তি দেন, তার জন্য আরশ বা সিংহাসন রয়েছে, ইত্যাদি। এখন এধরনের ঈশ্বর যদি মহাবিশ্ব তৈরি করে থাকেন, জীবন তৈরির পরিকল্পনা এবং নকশা প্রণয়ন করে থাকেন, প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে থাকেন তবে কিন্তু সেসব দাবিগুলো আমাদের পরীক্ষা করে যাচাই করতে পারার কথা। আমরা আজ জানি, যাচাইয়ের পর অনেক দাবিই ইতোমধ্যে ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরাই তা করেছেন। বিবর্তন তত্বই প্রমাণ করেছে জেমস আশারের ৪০০৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ঈশ্বরের বিশ্বসৃষ্টির কেচ্ছা কাহিনি কিংবা ২৩৪৮ খ্রিস্টপূর্বাব্দে নুহের প্লাবনের কেচ্ছা মিথ্যা এধরনের অনেক কিছুই ভবিষ্যতেও যে বিজ্ঞান ভুল প্রমাণ করবে না তা কে বলতে পারে? যেমন, নব্যনাস্তিকতাবাদী বিজ্ঞানীরা মনেই করেন, যিশুর ভার্জিন বার্থ, তার পুনরুত্থান, আত্মার অস্তিত্ব এবং মৃত্যুর পরে তার বেঁচে থাকা-ধার্মিকদের কাছ থেকে আসা এই দাবিগুলো আসলে প্রকারান্তরে বৈজ্ঞানিক দাবিই, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এর সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করা যাবে। রিচার্ড ডকিন্স তার শীর্ষ বিক্রিত বই ‘গড ডিলুশনে’ পরিষ্কার করেই বলেন, ‘বিনা পিতায় যিশু জন্মাতে পারেন কিনা তা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের অংশ, কোনো নৈতিকতা বা মূল্যবোধের প্রশ্ন নয়[২১]।
বিজ্ঞানীরা এখন বলেন, ঈশ্বরের প্রার্থনায় সাড়া দেওয়া কিংবা সত্যিকার ঈশ্বর কে–এই হাইপোথিসিসগুলো কিন্তু সহজেই পরীক্ষা করে নির্ণয় করা যায়। যেমন, ধরা যাক একটি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হলো যেখানে মৃত্যুপথযাত্রী হিন্দু মুসলিম, বৌদ্ধ বা খ্রিস্টান রোগীর জন্য আলাদা করে প্রার্থনার ব্যবস্থা করা হবে। দেখা গেল ইসলামি প্রার্থনাতেই রোগী কেবল ভালো হচ্ছে কিংবা মুসলিম রোগী পটাপট সেরে উঠছে, আর বাকিরা পটল তুলছে, তাহলে সাথে সাথে আমরা বুঝে নিতাম ইসলামি আল্লাহই সত্যিকার ঈশ্বর, কারণ তিনিই প্রার্থনায় সাড়া দিচ্ছেন। কিন্তু এ ধরনের ঘটনা ঘটে নি। বরং মায়ো ক্লিনিক, ডিউক ইউনিভার্সিটির সাম্প্রতিক গবেষণাগুলো প্রার্থনার সাথে রোগীর ভালো হওয়ার কোনো সম্পর্কই খুঁজে পায় নি[২২]।
আব্রাহামিক ধর্মগুলোতে বর্ণিত ঈশ্বর পরস্পরবিরোধী একটি সত্বা। যেমন বাইবেলের ধারণা অনুযায়ী ঈশ্বর অদৃশ্য (Col. 1:15, ITi 1:17, 6 : 16), এমন একটি সত্ত্বা যাকে কখনও দেখা যায় নি (John 1: 18, IJo 4 : 12)। অথচ বাইবেলেরই বেশ কিছু চরিত্র যেমন মুসা (Ex 33 : 11, 23), আব্রাহাম, জেকব (Ge. 12 : 7,26 : 2, Ex 6: 3) ঈশ্বরকে দেখতে পেয়েছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে। ঈশ্বর পরিষ্কার করেই বাইবেলে বলেছেন- ‘তোমরা আমার মুখ দেখতে পাবে না, আমাকে দেখার পর কেউ বাঁচতে পারবে না’ (Ex 33 : 20)। অথচ, জেকব ঈশ্বরকে জীবন্ত দেখেছেন (Ge 32:30)। এগুলো তো পরিষ্কার স্ববিরোধিতা। ঠিক একই কথা বলা যায় হযরত মুহাম্মদের মেরাজের ক্ষেত্রেও। আরজ আলী মাতুব্বর তার সত্যের সন্ধান গ্রন্থে লিখেছেন,
এ কথায় প্রায় সকল ধর্মই একমত যে, ‘সৃষ্টিকর্তা সর্বত্র বিরাজিত’। তাহাই যদি হয়, তবে তাহার সান্নিধ্যলাভের জন্য দূরে যাইতে হইবে কেন? আল্লাহতালা কি ঐ সময় হযরত (দ.)–এর অন্তরে বা তাহার গৃহে, মক্কা শহরে অথবা পৃথিবীতেই ছিলেন না? পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলিয়াছেন-”তোমরা যেখানে থাক, তিনি তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন’ (সুরা হাদিদ-৪)। মেরাজ সত্য হইলে এই আয়াতের সহিত তাহার কোনো সংগতি থাকে কি?
আসলে আব্রাহামিক গড হিসেবে চিত্রিত ঈশ্বরের অনেক অ্যাট্রিবিউটকেই যুক্তির নিরিখে পরীক্ষা করে ভুল প্রমাণ করা যায় তা পদার্থবিজ্ঞানী ভিক্টর স্টেঙ্গর দেখিয়েছেন তার ‘গড-দ্য ফেইল্ড হাইপোথিসিস’ বইয়ে। তিনি বলেন–
আমি আমার বইয়ে ধার্মিকদের দেওয়া ঈশ্বরের অনুকল্প নিয়ে বৈজ্ঞানিকভাবেই আলোচনা করেছি, এবং আমার উপসংহার হচ্ছে আব্রাহামিক ঈশ্বর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেনি।
আবার, ঈশ্বরকে সংজ্ঞায়িত করতে যে ধরনের গুণাবলি আরোপ করা হয়, পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে সেগুলো পরস্পরবিরোধী কিনা। যেমন, কেউ যদি চারকোণা বৃত্তের অস্তিত্ব দাবি করে, সেটা যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যাবে এই ধারণাটি পরস্পরবিরোধী। একই কথা খাটে ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও। ধর্ম-দর্শন নির্বিশেষে যে বৈশিষ্ট্যগুলো দিয়ে ঈশ্বরকে সচরাচর মহিমান্বিত করা হয় সেগুলো সবই দেখা গেছে যুক্তির কষ্টিপাথরে খুবই ভঙ্গুর। যেমন, ঈশ্বরকে বলা হয় ‘পরম দয়াময়’ (all-loving) এবং সর্বশক্তিমান (all-powerful or omnipotent), fazo (perfect), সর্বজ্ঞ (omniscient) ইত্যাদি। কিন্তু সর্বশক্তিমত্তা (omnipotence) এবং সর্বজ্ঞতা (omniscience) যে একসাথে প্রযোজ্য হতে পারে না তা যুক্তিবাদীদের দৃষ্টি এড়ায় নি। যেমন, ক্যারেন ওয়েন্স তা সুন্দরভাবে নিম্নোক্ত পঙক্তিমালায় তুলে ধরেন।[২৩]
Can Omniscient God, who
Knows the future, find
The omnipotence to
Change His future mind?
কথা হচ্ছে, ঈশ্বর যদি সর্বজ্ঞ বা ‘অমনিসায়েন্ট’ হন, তবে ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা তিনি জানেন। আবার সর্বশক্তিমান হওয়ার কারণে তিনি তা পরিবর্তনেরও ক্ষমতা রাখেন। কিন্তু মুশকিল হলো, তিনি কী করবেন তা অনেক আগে থেকেই জানার মানে হলো শেষ সময়ে আকস্মিকভাবে মত পরিবর্তন করা তার পক্ষে অসম্ভব। আর তার পক্ষে কোনোকিছু অসম্ভব মানেই হচ্ছে তিনি সর্বশক্তিমান নন।
ঈশ্বর যে সর্বশক্তিমান নন, তা নিচের প্রশ্নটির সাহায্যে সহজেই দেখানো যেতে পারে–
যদি প্রশ্ন করা হয়– ঈশ্বর কি এমন কোনো ভারি পাথরখণ্ড তৈরি করতে পারবেন, যা তিনি নিজেই উত্তোলন করতে পারবেন না?
এ প্রশ্নটির উত্তর যদি হ্যাঁ হয়–তার মানে হচ্ছে ঈশ্বরের নিজের তৈরি পাথর নিজেই তুলতে পারবেন না, এর মানে তিনি সর্বশক্তিমান নন। আবার প্রশ্নটির উত্তর যদি না হয়, তার মানে হলো, সেরকম কোনো পাথর তিনি বানাতে পারবেন না, এটাও প্রকারান্তরে তার অক্ষমতাই প্রকাশ করছে। এ থেকে বোঝা যায়, অসীম ক্ষমতাবান বা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলতে কিছু নেই। দেখা গেছে, মানুষের কাছে যা যৌক্তিকভাবে অসম্ভব, তা ঈশ্বরও তৈরি করতে পারছেন না। ঈশ্বর পারবেন না চারকোণা বৃত্ত আঁকতে, ঈশ্বর পারবেন না কোনো ‘বিবাহিত ব্যাচেলর’ দেখাতে; কারণ এগুলো যৌক্তিকভাবে অসম্ভব।
ঈশ্বর যে পরম করুণাময় বা ‘অল লাভিং’ নন, তা বুঝতে রকেট সায়েন্টিস্ট হতে হয় না। আরজ আলী মাতুব্বর তার ‘সত্যের সন্ধানে’ গ্রন্থে বলেছেন–
কোন ব্যক্তি যদি একজন ক্ষুধার্তকে অন্নদান ও একজন পথিকের মাল লুণ্ঠন করে, একজন জলমগ্নকে উদ্ধার করে ও অন্য কাউকে হত্যা করে অথবা একজন গৃহহীনকে গৃহদান করে এবং অপরের গৃহ করে অগ্নিদাহ-তবে তাহাকে ‘দয়াময়’ বলা যায় কি? হয়ত তাহার উত্তর হইবে ‘না’। কিন্তু উপরোক্ত কার্যকলাপ সত্বেও ঈশ্বর আখ্যায়িত আছেন ‘দয়াময়’ নামে। … জীবজগতে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক বিদ্যমান। যখন কোন সবল প্রাণী দুর্বল প্রাণীকে ধরিয়া ভক্ষণ করে, তখন ঈশ্বর খাদকের কাছে দয়াময় বটে। কিন্তু তখন কি তিনি খাদ্যপ্রাণীটির কাছেও দয়াময়? যখন একটি সর্প একটি ব্যাঙকে ধরিয়া আস্তে আস্তে গিলিতে থাকে, তখন তিনি সর্পটির কাছে দয়াময় বটে। কিন্তু ব্যাঙটির কাছে তিনি নির্দয় নহেন কি? পক্ষান্তরে তিনি যদি ব্যাঙটির প্রতি সদয় হন, তবে সর্পটি অনাহারে মারা যায় না কি? … কাহারও জীবন রক্ষা করা যদি দ্যার কাজ হয় এবং হত্যা করা হয় নির্দয়তার কাজ, তাহা হইলে খাদ্য-খাদকের ব্যাপারে ঈশ্বর ‘সদয় এর চেয়ে নির্দয়’ই বেশী। তবে কতগুণ বেশী তাহা তিনি ভিন্ন অন্য কেউ জানে না, কেননা তিনি এক একটি জীবের জীবন রক্ষা করার উদ্দেশ্যে অসংখ্য জীবকে হত্যা করিয়া থাকেন। কে জানে একটি মানুষের জীবন রক্ষার জন্য তিনি কয়টি মাছ, মোরগ, ছাগল ইত্যাদি হত্যা করেন?… কেহ কেহ মনে করেন যে, ঈশ্বর সদয়ও নহেন এবং নির্দয়ও নহেন। তিনি নিরাকার, নির্বিকার ও অনির্বচনীয় এক সত্ত্বা। যদি তাহা নাই হয়, তবে পৃথিবীতে শিশুমৃত্যু, অপমৃত্যু, এবং ঝড়, বন্যা, মহামারী, ভূমিকম্প ইত্যাদি প্রাণহানির ঘটনাগুলির জন্য তিনিই কি দায়ী নহেন?
আরজ আলীর প্রশ্নমালা মানব মনের অন্তহীন সংশ্যবাদী চিন্তাকেই তুলে ধরেছে সার্থকভাবে। গ্রিক দার্শনিক এপিকিউরাস (৩৪১-২৭০ খ্রি.পূ.) সর্বপ্রথম ‘আর্গুমেন্ট অব এভিল’ (Argument of Evil)-এর সাহায্যে ‘ঈশ্বরের অস্তিত্বের অসাড়তা তুলে ধরেন এভাবে–
‘ঈশ্বর কি অন্যায়-অবিচার-অরাজকতা নিরোধে ইচ্ছুক, কিন্তু অক্ষম?
তাহলে তিনি সর্বশক্তিমান নন।
তিনি কি সক্ষম, কিন্তু অনিচ্ছুক?
তাহলে তিনি পরম দয়াময় নন, বরং অপকারী সত্বা।
তিনি কি সক্ষম এবং ইচ্ছুক-দুটোই?
তাহলে অন্যায়-অবিচার-অরাজকতা পৃথিবীতে বিরাজ করে কীভাবে?
তিনি কি সক্ষমও নন, ইচ্ছুকও নন?
তাহলে কেন তাকে অযথা ‘ঈশ্বর’ নামে ডাকা?’
অকাট্য এই যুক্তি। The Oxford Companion to Philosophy স্বীকার করেছে যে, সনাতন আস্তিকতার বিরুদ্ধে ‘আর্গুমেন্ট অব এভিল’ বা মন্দের যুক্তি সবচেয়ে শক্তিশালী মারণাস্ত্র, যা কেউই এখন পর্যন্ত ঠিকমতো খণ্ডন করতে পারে নি[২৪]। এ তো নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে, প্লেগ, মহামারী, খরা, বন্যা, সুনামির মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে লক্ষ কোটি নিরপরাধ নারী-পুরুষ এবং শিশুর মৃত্যুর ব্যাপারে মানুষকে কোনোভাবেই দায়ী করা চলে না। এ সমস্ত অরাজকতার অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে, ঈশ্বর একটি অপকারী সত্ত্বা। কারণ ‘সর্বজ্ঞ’ ঈশ্বর আগে থেকেই জানতেন যে, সুনামির ঢেউ আছড়ে পড়ে তার নিজের সন্তানদের হত্যা করবে, তাদের স্বজনহারা করবে, গৃহচ্যুত করবে, ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, ঘরবাড়ি ধ্বংস করে এক অশুভ তাণ্ডব সৃষ্টি করবে। অথচ আগে থেকে জানা থাকা সত্ত্বেও সেসব প্রতিরোধে কোনো ব্যবস্থাই তিনি নিতে পারেন নি। এ থেকে প্রমাণিত হয় ঈশ্বর এক অক্ষম সত্ত্বা বই কিছু নয়। দার্শনিক পল কার্জ তার ‘ধর্মীয় দাবি সম্বন্ধে যে কারণে আমি সংশয়বাদী’ প্রবন্ধের একটি অংশে ‘আর্গুমেন্ট অব এভিল’ নিয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করেছেন। এছাড়া, মুক্তমনায় বহু লেখক বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা এবং ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা আসলে পরস্পরবিরোধী[২৬]।
ভিক্টর স্টেঙ্গর পেশায় হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান’ বিভাগের ইমিরিটাস অধ্যাপক এবং কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালযের দর্শনের সংযুক্ত অধ্যাপক (Adjunct Professor। তিনি একবিংশ শতাব্দীর এই নতুন দিনের নাস্তিকতাবাদী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ। ভিক্টর স্টেঙ্গর তার ‘গড-দ্য ফেইল্ড হাইপোথিসিস’ বইয়ে সর্বজ্ঞ (Omniscient), পরম করুণাময় (Omnibenevolent) এবং সর্বশক্তিমান (Omnipotent) ঈশ্বর (30 God) থাকাটা যে যৌক্তিকভাবে অসম্ভব তা দেখিয়েছেন[২৭]। একই ধরনের উপসংহারে পৌঁছিয়েছেন মাইকেল মার্টিন এবং রিকি মনিয়ার তাঁদের The impossibility of God বইয়ে[২৮]। কাজেই ঈশ্বরের কোনো বৈশিষ্ট্য যৌক্তিকভাবে পরীক্ষা করে বাতিল করে দেওয়া যাবে না, কিংবা বিজ্ঞান এ ব্যাপারে কোনো অভিমত দিতে পারে না–তা কিন্তু এখন আর ঠিক নয়। বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানের দার্শনিক রিচার্ড ডকিন্সও মনে করেন ধার্মিকদের দেওয়া ঈশ্বরের অনেক সংজ্ঞাই টেস্টেবল হাইপোথিসিস, এবং তিনি তার সাম্প্রতিক’ গড ডিলুশন’ বইয়ে এর অনেকগুলোই খণ্ডন করেছেন। এরকম অনেক অনুকল্পের বেশকিছু পরীক্ষা এখনই করা যায়, বাকিগুলো হয়ত প্রযুক্তি উন্নত হলে করা যাবে। অন্তত আব্রাহামিক ধর্মগুলোর ঈশ্বরের যে সংজ্ঞায়ন ধর্মগ্রন্থগুলোতে পাওয়া যায়, তা যে অবৈজ্ঞানিক এবং ভ্রান্ত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সেজন্যই ভিক্টর স্টেঙ্গর তার নিউ এথিজম বইয়ে বলেন–
The new atheists firmly assert that the personal, abrahamic God is a scientific hypothesis that can be tested by the standard method of science. And we have seen that it has failed the test.
এবারে নব্য নাস্তিকতা-বিরোধী কিছু উদাহরণের সাথে পাঠকদের পরিচিত করিয়ে দেওয়া যাক। নব্য নাস্তিকদের বিজ্ঞানের তথ্য-উপাত্ত, জ্ঞান দিয়ে ঈশ্বর আলোচনার একজন কড়া সমালোচক খ্রিস্টান ধর্মবেত্তা ডেভিড মার্শাল। ‘The Truth behind the New Atheism’ বলেন[২৯],
এই নব্য নাস্তিকরা বাস্তবতার বিভিন্ন দিক একেবারেই বুঝতে পারে না। প্রথমত, বোকা নাস্তিকদের বিজ্ঞানের সীমারেখা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। দ্বিতীয়ত, তাদের তত্বগুলো অসংখ্য বাস্তবতাকে সরাসরি উপেক্ষা করে। তৃতীয়ত, গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা থেকে তারা সবসময় নিজেদের বিরত রাখে। চতুর্থত, তাদের তত্ত্বকে ভরাডুবির হাত থেকে বাঁচাতে তারা চমৎকার এক ছলনার আশ্রয় নেয়, সেই ছলনা হলো–’মনে করি’।
বিজ্ঞানের সীমারেখা বুঝতে অপারগ একজন বোকা কিংবা চালাক নাস্তিকের নাম উল্লেখ করেন নি, মার্শাল। নব্য নাস্তিকদের বই, তাদের বিভিন্ন প্রবন্ধ, ইউটিউবে থাকা শতশত ভিডিও লেকচারে আমরা কখনোই তাদের বলতে শুনি নি, যে বিজ্ঞানের সীমারেখা অসীম। অদ্ভুত ব্যাপার হলো, এদের লেখা বইগুলোতেই বরঞ্চ সংগীত, ছবি, কবিতা, নারী-পুরুষের ভালোবাসার সম্পর্কসহ আরও অসংখ্য প্রকৃতি প্রদত্ত অবৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে চমৎকার মনোমুগ্ধকর আলোচনা পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে আমাদের[৩০]। আমরাও গান ভালোবাসি, ভালোবাসি ব্লগালোচনা, কবিতা, ফুল, ভালোবাসি ভালোবাসতে, কিংবা ভালোবাসা পেতে। কিন্তু একই সাথে অন্যান্য অনেকের মতো মনে করি না যে, এই অবৈজ্ঞানিক বিষয়গুলো বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া চমৎকারভাবে উপভোগ করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে, মহাকবি কিটস একবার নিউটনের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছিলেন যে আলোকের সূত্রের মাধ্যমে রঙধনুর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি রঙধনুর সৌন্দর্যকেই ক্ষুণ্ণ করে দিয়েছেন। অথচ কিটসই আবার অন্য এক প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, ‘সত্যই সুন্দর!’ আরেকবার, পদার্থবিদ ফাইনম্যানকে তার এক শিল্পী বন্ধু একটা ফুল হাতে নিয়ে বলেছিলেন, ‘একজন শিল্পী হিসেবে আমি এই ফুলের সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম, আর তোমরা বিজ্ঞানীরা এটাকে ভেঙেচুরে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এর সৌন্দর্যকেই নষ্ট করে দাও। এর উত্তরে ফাইনম্যান বলেছিলেন যে, একজন শিল্পী ফুলে যে সৌন্দর্য দেখতে পান, তিনিও সেই একই সৌন্দর্য দেখতে পান, কিন্তু উপরন্তু তিনি ফুলের ভেতরকার সৌন্দর্যকেও দেখতে পান, যেমন কীভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ দ্বারা ফুলের পাপডি গঠিত হয়, কীভাবে বিবর্তনিক উপযোজনের কারণে কীটপতঙ্গকে আকর্ষণ করার জন্য ফুলের সুন্দর রঙের সৃষ্টি হয়েছে, এইসব, যা থেকে তার শিল্পী বন্ধু বঞ্চিত’[৩১]।
আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কথাই ধরি। গানের ফিজিক্স বোঝার মাধ্যমে একে আরও ভালোভাবে উপভোগ, উপস্থাপন করার সূক্ষতা উদ্ভাবনের পাশাপাশি, আবিষ্কৃত হয়েছে নানা যন্ত্রপাতি। রেকর্ডিং করার উপায় আবিষ্কারের মাধ্যমে যেকোনো পরিস্থিতিতে গান যে কাউকে সঙ্গ দিতে পারে। বিজ্ঞানের কারণে আমরা নিজেরাও এখন ছবি তুলে/ এঁকে সেগুলো ফ্লিকারে আপলোড করার মাধ্যমে সবার সাথে শেয়ার করতে পারি। দুনিয়ার প্রায় সকল কবিতা, গল্প খুব কিছু দিনের মধ্যেই চলে আসবে ইন্টারনেটে। স্টিফেন হকিংযের নতুন বই পড়ার জন্য মানুষের এখন আর বছর খানেক অপেক্ষা করতে হয় না, তারা আমাজনে চট করে অর্ডার দিয়ে পরের দিন হাতের কাছে পেয়ে যায়।
কোনো ধরনের উদাহরণ না দিয়ে মার্শাল তার তৃতীয় ও চতুর্থ দাবি, বাস্তবতাকে পাশ কাটানো, এবং ‘মনে করি’ ব্যাপারটাকে কটাক্ষ করে কী বোঝাতে চেযেছেন সেটা বোধগম্য হলো না কোনোভাবেই।
বুদ্ধিদীপ্ত নকশা (Intelligent Design) নামক ছদ্মবিজ্ঞানের এক মুখপাত্র ডেভিড বারলিনস্কি (David Berlinski) বিজ্ঞানীদের চরিত্র নিয়ে গবেষণার পর প্রবন্ধে লেখেন, অধিকাংশ বিজ্ঞানীরা গোঁয়ার, অন্তঃসারশূন্য, রাজনীতিতে অপরিপক্ক, অলস এবং অহংকারী[৩২]। তথ্যসূত্র ছাড়াই বেশ কিছু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের লাইন তুলে ধরে তিনি বলেন, বিজ্ঞানীরা সবকিছু বিশ্বাস করতে প্রস্তুত[৩৩]। অবশ্যই বিজ্ঞানীরা যেকোনো কিছু বিশ্বাস করতে প্রস্তুত যদি সেটা বিশ্বাস করার মতো পর্যাপ্ত প্রমাণ থাকে। হ্যাঁ! মাঝে মাঝেই বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ধারণা পড়ে আমাদের সেটা অর্থহীন, অসম্ভব বলে মনে হয়, কিন্তু সেটার দোষ তো বিজ্ঞানীদের না। ব্যাপারগুলো আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে অর্থহীন বলে মনে হলেও বাস্তবে তা নয়। কারণ প্রতিটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার সম্পন্ন হয় বস্তুনিষ্ঠ নৈর্ব্যক্তিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিটি আবিষ্কার বা বৈজ্ঞানিক তত্ব আরও অসংখ্য তত্বের সমন্বয়ে গঠিত হয়। প্রতিটি বৈজ্ঞানিক ধারণা যিনি আবিষ্কার করেছেন শুধু তার জন্য সত্য না, বরঞ্চ সেটা পৃথিবীর যেকোনো ল্যাবরেটরিতে, যেকোনো মানুষ দ্বারা স্বাধীনভাবে পরীক্ষণযোগ্য।
গ্রুপ মেইলে হঠাৎ করেই একবার ধর্ম-নিধর্ম আলোচনায় একজন বিশাল এক মেইল করে বসলেন। আস্তিক-নাস্তিকতা বিষয়ে অনেক বই তিনি পড়েছেন, এই দাবি-সম্বলিত বিশাল মেইলে নাস্তিকদের উদ্দেশ্য করে বলা কথাটির সারমর্ম ঈশ্বরের মতো একজন যিনি স্থান, কালের ঊর্ধ্বে তার অস্তিত্ব মাপার জন্য পার্থিব পরিমাপ, ওজন, গণিত ব্যবহারের মতো হাস্যকর কিছুই আর হতে পারে না। নাস্তিকতার বিপক্ষে প্রচলিত এই কথাটি অযৌক্তিক হলেও অসংখ্য বিজ্ঞানী দুঃখজনক ভাবে এটি সমর্থন করে থাকেন। রক্ষণশীল লেখক এবং বক্তা দিনেশ ডি’সুজা জীববিজ্ঞানী ডগলাস এরউইনকে উদ্ধৃত করে বলেন, ‘বিজ্ঞানের অন্যতম একটি নিয়ম বা ধারা হচ্ছে, সকল ধরনের মিরাকলের অস্তিত্ব অস্বীকার করা”[৩৪]। তার মানে কী এই দাঁড়ালো যে, সত্যিকার অর্থেই ব্যাখ্যাতীত মিরাকলের প্রমাণ পাওয়া গেলে বিজ্ঞান সেটা অস্বীকার করবে? কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের যুক্তিমনস্ক মানুষেরই দিনেশ ডিসুজার বক্তব্যকে সমর্থন করার কথা না।
দিনেশ সু’জা জীববিজ্ঞানী ব্যারি পালেভিটজকে উদ্ধৃত করে আরও বলেন, প্রাকৃতিক মহাবিশ্বকে জানার জন্য অতিপ্রাকৃত ব্যাখ্যা এমনিতেই বাদ দিয়ে দেওয়া হয়[৩৫]। এখন, যদি অতিপ্রাকৃত কোনো ব্যাখ্যা সত্যিই চমৎকারভাবে কাজ করতে থাকে তখন সেটাও কি বাদ দিয়ে দেওয়া হবে? কেন?
শুধু দিনেশ ডি’সুজার মতো ব্যক্তিরাই কেবল নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস বিজ্ঞান এবং অতিপ্রাকৃত ঘটনা সম্বন্ধে একই ধরনের অযৌক্তিক ধারণা পোষণ করে[৩৬]–
প্রাকৃতিক মহাবিশ্বকে জানার জন্য বিজ্ঞান ব্যবহার করা হয়। প্রাকৃতিক কারণের আলোকে প্রাকৃতিক মহাবিশ্ব ব্যাখ্যা করা পর্যন্তই বিজ্ঞানের সীমারেখা অতিপ্রাকৃত ব্যাপার নিয়ে বিজ্ঞানের বলার কিছু নেই। সুতরাং ঈশ্বর আছে কি নেই, এমন প্রশ্ন বিজ্ঞানে অবান্তর, যতক্ষণ পর্যন্ত বিজ্ঞান তার নিরপেক্ষতা ধরে রাখে।
অথচ খোদ ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস-এর সদস্যদের মধ্যে মাত্র সাত শতাংশ ঈশ্বরে বিশ্বাসী[৩৭], সুতরাং বাকিরা হয় নাস্তিক কিংবা অজ্ঞেয়বাদী, যদিও এদের কারোরই অধিকাংশ ধার্মিক আমেরিকানদের সাথে দার্শনিক ধর্মযুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার বাসনা নেই।
বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক (এবং নাস্তিক) স্টিফেন জে গুল্ড তার শেষ বইয়ে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে একটি সমঝোতা আনার চেষ্টা করেছেন। বিজ্ঞান ও ধর্মকে তিনি চিহ্নিত করেছেন দুইটি স্বতন্ত্র বল [Non-Overlapping Magisteria (NOMA)] হিসেবে, যেখানে বিজ্ঞান তার নিজস্ব বলয়ে কাজ করে প্রাকৃতিক মহাবিশ্বকে বুঝতে, আর ধর্ম অন্য বলমে কাজ করে নৈতিকতা বজায় রাখতে[৩৮]।
অসংখ্য সমালোচক গুল্ডের বক্তব্য পর্যালোচনা করে বলেছেন, তিনি ধর্মকে ‘নৈতিকতার দর্শন হিসেবে সংজ্ঞায়িত করছেন। যদিও বাস্তবতায় আমরা দেখতে পাই, কেবল নৈতিকতার দর্শনেই ধর্মের কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ নয়। ধর্ম প্রাকৃতিক মহাবিশ্ব সম্বন্ধেও নানা ধরনের মতামত প্রদান করে। ধর্ম মতামত করে জীবনের উৎপত্তি নিয়ে, মতামত প্রদান করে মহাবিশ্বের সূচনা নিয়ে-যেই দাবিগুলো সত্যতা কোনো নৈতিক ধর্ম দিয়ে নয়, বরং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় জানা সম্ভব। রিচার্ড ডকিন্স তার ‘গড ডিলুশন’ বইয়ে এবং অন্যত্র গুল্ড প্রস্তাবিত স্বতন্ত্র বল্য তত্বের বিরুদ্ধে জোরালো যুক্তি দিয়েছেন একাধিকবার[৩৯]। ডকিন্স ধর্মীয় বিশ্বাস প্রসূত কল্পকাহিনিগুলোকে বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাইয়ের বাইরে রাখার চেষ্টাকে অসৎ মনোবৃত্তির পরিচায়ক মনে করেন। তার ভাষায়, ধর্মে যেসমস্ত অলৌকিক গল্প কাহিনি দিয়ে সাধারণ মানুষকে বোকা বানানো হয়, সেই গল্পগুলোর মধ্যে ব্যবহার করা হয় বিজ্ঞানের উপকরণ; আর বিজ্ঞান যখন এইসব গাঁজাখুরি গল্প-কাহিনির সত্যতা এবং সম্ভাব্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে তখনই বলা হয়, বিজ্ঞান ধর্মে নাক গলাচ্ছে। আপাতদৃষ্টিতে স্বতন্ত্র বলয়ের প্রবক্তাদের মনে হয় শান্তিকামী, কিন্তু মিথ্যাকে মেনে নিয়ে যে শান্তি, তা কাম্য হওয়া উচিত নয়।
এবার আসা যাক নৈতিকতা প্রসঙ্গে মানব সভ্যতার পথ-পরিক্রমায় ধর্ম এই একটি ক্ষেত্রেও যে খুব অবদান রেখেছে বা রেখে চলেছে তাও নয়। এটি সমর্থন করেছে দাস প্রথা, সমর্থন করেছে রাজার একচ্ছত্র অধিকার, সমর্থন করেছে মৃত্যুদণ্ড, অঙ্গচ্ছেদন, হরণ করেছে নারীর স্বাধীনতা। ইরানসহ আরও কিছু মুসলিম দেশে এখনও ইসলামি শরিয়া অনু্যায়ী মেয়েদের পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হয়। প্রতিবেশী দেশ ভারতে এক সময় সতীদাহ প্রথা অনুসারে স্বামীর সাথে জীবন্ত পোড়ানো হতো স্ত্রীকে। নানা সময়ে নানা জায়গায় ধর্ম ওষুধ গ্রহণ করতে বাধা দিয়েছে, বাধা দিয়েছে জন্মনিয়ন্ত্রক বড়ি ব্যবহারে। সর্বাধিক এইডস আক্রান্ত আফ্রিকায় এইডসের সংক্রামক থেকে নিজেকে রক্ষা করার অন্যতম উপায় যৌনমিলনের আগে কনডম ব্যবহার, সেটাকেও একসময় বাধা দিয়েছিল চার্চ।
মানুষকে মিথ্যা বলা থেকে বিরত রাখা, সৎ রাখা কিংবা খুনাখুনি থেকে বিরত রাখার জন্য উপরওয়ালার ভয়ের প্রয়োজনীয়তা কতোটুকু সেটাও ভাববার বিষয়। বইয়ের পরবর্তী একটি অধ্যায়ে এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা আমরা করব। কিন্তু একটি কথা এখানেই বলে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি। বাস্তবতা হলো, সাধারণ নৈতিক ব্যাপারগুলো (সত্য কথা বলা, সৎ থাকা, হত্যা না করা) বড় বড় ধর্ম শুরু হওয়ার বহু আগে থেকেই মানবসমাজে প্রচলিত ছিল। সুতরাং ধর্মের যদি কোনো উপকারিতা থেকেও থাকে, সেগুলো ধর্ম ছাড়াও সমানভাবে থাকবে, এমন আশা করাটা অযৌক্তিক নয়[৪০]।
আমেরিকার ন্যাশনাল অ্যাকাডেমির সদস্যদের মধ্যে যারা মনে করে থাকেন, বিজ্ঞানের ঈশ্বর সম্পর্কে বলার কিছু নেই, তারা আসলে চোখের সামনে থাকা বাস্তবতাকে উপেক্ষা করছেন[৪১]। হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, ডিউক ইউনিভার্সিটি এবং মায়ো ক্লিনিকের মতো পৃথিবী বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞানীরা প্রার্থনার কোনো উপকারিতা আছে কিনা তা নিয়ে গবেষণা করছেন। এখন এই গবেষণাগুলোতে প্রাপ্ত ফলাফল যদি ধনাত্মক হয় এবং এগুলো যদি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের মানুষের উপর একই ধরনের ফল প্রদান করে তাহলে আমরা নব্য নাস্তিকরা অবশ্যই ঈশ্বর বলে একজন থাকতে পারে, এমন ধনাত্মক ধারণা নিয়ে আরও সূক্ষ গবেষণায় আগ্রহী হবো।
হ্যাঁ! উপরের গবেষণাগুলোয় প্রার্থনা কাজ করে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি[৪২]। তবে সেটা ব্যাপার না, ব্যাপার হলো পাওয়া যেতে পারত। তখন ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস-এর সদস্যদের মতামত কী হতো? আমরা কি সেই গবেষণা বাতিল ঘোষণা করতাম? করতাম না। ঈশ্বরের মতো একজন, যিনি মানুষের প্রার্থনা শোনেন এবং সেটা কবুল করেন তাকে অবশ্যই বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব। কারণ প্রার্থনা কবুলের ফলাফল অনেকসময় পৃথিবীতেই পাওয়া যায়। পৃথিবীতে যখন পাওয়া যায় তখন সেটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।
তবে ধর্মবেত্তা এবং হুজুরেরা এখন অতিপ্রাকৃত বিষয় পরীক্ষায় বিজ্ঞানকে যতই তাচ্ছিল্য করে থাকুক না কেন, আজকে যদি প্রার্থনার সরাসরি উপকারিতা (প্ল্যাসিবো নয়) বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হতো তাহলে আমরা অসংখ্য টিভি-চ্যানেল, পত্র-পত্রিকায় বড় করে খবর দেখতাম, মাওলানা অমুক আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণকে স্বাগত জানিয়েছেন!?[৪৩]
.
বিজ্ঞানও কি বিশ্বাসের ওপর প্রতিষ্ঠিত?
অনেকেই বলে থাকেন, বাস্তব জীবনের সকল ঘটনা যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব, এমন একটি অন্ধবিশ্বাস লালন করে থাকে নাস্তিকরা, বিশেষ করে নব্য নাস্তিকরা। চারপাশকে তবে কী হিসেবে মনে করা উচিত? অযৌক্তিক? আসলে জগৎ যৌক্তিক কিংবা অযৌক্তিক কিছুই না। যৌক্তিক কিংবা অযৌক্তিক হলো মানুষের মন, মানুষ। আমরা যখন কোনো বিষয়ের ওপর নিজের মতামত প্রকাশ করব তখন আমাদের চয়ন করা শব্দগুলো হতে হবে অর্থবোধক, আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথ হতে হবে যৌক্তিক। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি পদার্থ বিজ্ঞান সেমিনারের কথা। সেমিনারের মূল বিষয় মহাবিশ্বের সূচনা। পৃথিবীর সেরা পদার্থবিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে নিজেদের গবেষণা, গবেষণার ফলাফল তুলে ধরছেন। তাদের প্রতিটি গবেষণা পদার্থবিজ্ঞানের অন্যান্য সূত্রকে আমলে নিয়ে হয়েছে, অর্থাৎ সেগুলো বর্তমান বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সাথে ধারাবাহিক। এমন সময় মিস্টার যদু মঞ্চে উঠে বললেন, মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে ক্রিমিয়াম নামক এক এলিয়েনের কারণে। এক ছুটির দিনে ঘরে বসে বিয়ার তৈরির সময় হঠাৎ সেখানে বিস্ফোরণ হয়, আর এই বিস্ফোরণই আসলে তথাকথিত ‘বিগব্যাং’-যার মধ্য দিয়ে সৃষ্টি হয়েছে আমাদের এই মহাবিশ্বের।
সঠিক উত্তর পাওয়ার জন্য কোন প্রক্রিয়াটি সঠিক বলে আপনার মনে হয়? পল ডেভিস বিখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী। পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে ভালো তাত্ত্বিক কাজ আছে তারা সেইসাথে তিনি একজন বিখ্যাত বিজ্ঞান লেখকও বটে। কিন্তু পল ডেভিস মাঝে মধ্যেই পদার্থবিজ্ঞানের বইপত্রগুলো পাশে তুলে রেখে ঢুকে পড়তে চান আধ্যাত্মিক জগতে। পল ডেভিস ২০০৭ সালে নিউ ইয়র্ক টাইমস-এ লেখা একটি প্রবন্ধে বিজ্ঞানকে আখ্যায়িত করেন ধর্মের মতো নতুন এক ধরনের বিশ্বাস ব্যবস্থা হিসেবে। ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন[৪৪], ‘প্রকৃতি যৌক্তিক এমন একটি বিশ্বাসকে পুঁজি করে বিজ্ঞান এগিয়ে চলে।’ তিনি আরও বলেন, ‘যদি ঈশ্বর থেকেই থাকে সেক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ করে পাওয়া সিদ্ধান্ত নয়, বরঞ্চ ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতাই পারবে তা জানতো।’
কেন? বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কাজ করে। ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা যাই হোক না কেন, সেটা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব। আর যখনই কিছু পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে তখনই বিজ্ঞান সেটি নিয়ে কাজ করতে সক্ষম। বাংলাদেশেই আমরা অনেক আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন পীর ফকিরের কথা শুনি, যারা ফুঁ দিয়ে মানুষের রোগ নিরাময় করে দিতে পারেন। এখন ফুঁ দেওয়াটা পীর ফকিরের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা, কিন্তু আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার ফলে রোগীর রোগ নিরাময় তো আমরা নিজের চোখে দেখতে পারি। সুতরাং বিজ্ঞান দিয়ে আমরা জানতেও পারব, আসলেই রোগ সারে কিনা। আমরা তার সামনে একশজন রোগী নিয়ে বসাব, তিনি ফুঁ দিবেন, তারপর পরীক্ষা করে দেখব আসলেই একশ জনের রোগ ভালো হয়ে গিয়েছে কিনা।
এছাড়াও ভিক্টর স্টেঙ্গর তার ‘নিউ এইথিজম’ বইয়ে প্রচুর সংখ্যক ব্যক্তিগত ধর্মীয় অভিজ্ঞতার উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন, কীভাবে সেগুলোও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার আওতাধীন।
ধর্মবেত্তা জন হট বলেন[৪৫], বিবর্তন মানুষের অনুভব করার ক্ষমতাকে ব্যাখ্যা করতে পারে না–আমাদের বিভিন্ন বিষয় অনুভবের ক্ষমতা দেখলে বোঝা যায় বিবর্তন ছাড়াও অন্য এক শক্তি আমাদের ওপর কাজ করেছে যার ফলে আমরা চিন্তা করতে পারি, যার ফলে আমাদের মন অন্য সবার থেকে আলাদা।
তার এই কথা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মতামত। বিবর্তনের ফলে বিভিন্ন মানসিক ক্ষমতার উদ্ভব কীভাবে হয়েছে সেটা হট জানেন না; তার মানে এই না যে, কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তি তা করেছে। এটা অজ্ঞতাপ্রসূত যুক্তি (Argument From Ignorance)। আর বিবর্তন মানুষের অনুভূতিকে ব্যাখ্যা করতে পারবে না কেন? এই বিষয়ে ইতোমধ্যেই উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কাজ হয়েছে এবং এমন কোনো বিপরীত যুক্তি পাওয়া যায় নি যার ফলে আমরা বলতে পারব এই চিন্তা-ভাবনা করা, অভিজ্ঞতা থেকে জ্ঞান আহরণ, অনুভব করার মতো বিষয় বিবর্তন ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।
.
আমরা কি আমাদের মনকে বিশ্বাস করতে পারি?
ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে সন্দেহ জেগেছে? চারপাশে তাকাও তারপর চিন্তা করো গভীরভাবে। তাহলেই তাকে উপলব্ধি করতে পারবে, দূর হয়ে যাবে সকল সংশয়–এমন কথা হরহামেশাই শুনতে পাই আমরা। সত্যের সন্ধান পাওয়ার জন্য মনের ওপর শতভাগ আস্থা জ্ঞাপনের আবেদন জানান মসজিদের ইমাম থেকে শুরু করে, ইসলামিক টিভির আলোচক, চার্চের ফাদার সবাই।
মনকে কেন আমরা বিশ্বাস করব তার সবচেয়ে ভালো উত্তর দিতে সক্ষম ধর্ম। আমরা মনকে বিশ্বাস করব এই কারণে যে, বস্তুবাদী জ্ঞান, যুক্তি এ সবকিছু ছাড়িয়ে আমাদের মন এক মহাশক্তিধরের গুণাবলি সত্য, সুন্দর দ্বারা আবদ্ধ।
হিটলার বিশ্বাস করেছিলেন তার মনকে, যে মন তাকে বলেছিল জার্মান জাতির গৌরব ফিরিয়ে আনার জন্য সকল ইহুদিকে হত্যা করতে হবে। গোলাম আজম থেকে শুরু করে টেলিভিশন চ্যানেলের কল্যাণে আজকের খ্যাতনামা ইসলামি চিন্তাবিদ মাওলানা আবুল কালাম আজাদরা বিশ্বাস করেছিলেন ‘সকল মুসলমান ভাই ভাই’ তত্বে। তাদের মন বলেছিল পাকিস্তান রক্ষা করতে হবে। বলেছিল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ইসলামি রাষ্ট্র সমুন্নত রাখতে গেলে হাত একটু ময়লা করতেই হবে। তাই ধর্মের দোহাই দিয়ে নিজের ভাইকে হত্যা করেছিল তারা বিনা দ্বিধায়, নিজের বোনকে ধর্ষণ করেছিল বিনা গ্লানিতে।
নব্য নাস্তিকরা অন্যের মন তো দূরের কথা, নিজের মনকেও বিশ্বাস করে না। তাই আমরা কেবল হই বিজ্ঞান ও যুক্তির দ্বারস্থ। অন্যদিকে আমাদের ধার্মিকরা সিদ্ধান্তে পৌঁছান কেমন করে? মনে মনে চিন্তা করে। অবশ্য ধর্মগ্রন্থে লেখা থাকলেও বহু ধার্মিকই ধর্মগ্রন্থের নৃশংসতাগুলোকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন না। চললে মুসলিম তথা মুহাম্মদের অনুসারীরা ইহুদি নাসারাদের যেখানে দেখত সেখানেই হত্যা করত, খ্রিস্টানরা নিজের সন্তান কথা না শুনলে তাকে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করত, জোসেফ স্মিথের হুকুম অনুসারে মরমনরা যত জন ইচ্ছা স্ত্রী রাখতে পারত (জোসেফ স্মিথকে ঈশ্বর হুকুম করছে, একজন মানুষ যতজন ইচ্ছা স্ত্রী গ্রহণ করতে পারে), হিন্দুরা মুসলমানের ছোঁয়া লাগলে গঙ্গাজল দিয়ে স্নান করার জন্য দৌড় লাগাত। তবে একজনও যদি করে থাকেন সেটার দায়ভার বর্তায় ধর্মের ওপরেই। বিল মার তার ডকুমেন্টারি রিলিজুলাস-এ চমৎকারভাবে ব্যাপারটি বলেছিলেন। মানুষ প্রথমে নিজ স্বার্থ চরিতার্থের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তারপর যায় ধর্মগ্রন্থের কাছে। সেখান থেকে তার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে এমন আয়াত খুঁজে বের করে এবং কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ কারণেই জঙ্গিরা নিরীহ জনগণ হত্যাকে কোরআনের আয়াত দিয়ে সঠিক কাজ হিসেবে, ঈশ্বরের কাজ হিসেবে প্রচার করে। এ কারণেই ইরানের আয়াতুল্লাহ গোষ্ঠী মেয়েদের পাথর ছুঁড়ে হত্যা করে।
বিশ্বাসের সবচেয়ে ভয়ংকর দিক এটাই। চেক এন্ড ব্যালেন্স-এর কোনো উপায় নেই। আয়াতুল্লাহ মেয়েদের হত্যা করে পাথর ছুঁডে, তারপর সবাইকে দেখিয়েছেন কোরআনের আয়াত। ধর্মবিশ্বাসীরা সেই আয়াতকে অস্বীকার করতে পারবে না, পারে নি, তাই আজকে ইরানে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই হয় এই ঘৃণ্য মানবতাবিরোধী কাজ। বিজ্ঞানী ওয়াইনবার্গ একবার একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন[৪৬]–
ধর্ম মানবতার জন্য এক নির্মম পরিহাস। ধর্ম মানুক বা নাই মানুক, সবসময়ই এমন অবস্থা থাকবে যে ভালো মানুষেরা ভালো কাজ করছে, আর খারাপ মানুষেরা খারাপ কাজ করছে। কিন্তু ভালো মানুষকে দিয়ে খারাপ কাজ করানোর ক্ষেত্রে ধর্মের জুড়ি নেই।
প্রাচীন ধর্মগুরুদের মনের মাধুরী মিশিয়ে লেখা কথায় নতুন ধর্মগুরুরা যেমন ইচ্ছা ব্যাখ্যা আরোপ করে। আর তার ওপর, শুধু আমার মন চাইছে সেই যুক্তিতে, দলে দলে মানুষ স্থাপন করে সংশয়হীন আস্থা। বিনা প্রশ্নে স্থাপন করে দৃঢ় অন্ধবিশ্বাস। যার কারণেই আমরা মানব-ইতিহাসের করুণতম বিপর্যযগুলো ঘটতে দেখি। আমরা দেখি ধর্ম-যুদ্ধের নামে জীবন দিচ্ছে কোটি কোটি মানুষ, নিশ্চিহ্ন হচ্ছে শহর-নগর-সভ্যতা। প্রস্তরাঘাতে হত্যা করা হচ্ছে নিরীহ নারী-পুরুষ শিক্ষা আর জ্ঞানের সকল পথ বন্ধ করে পুরো জাতিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বর্বর অন্ধকারের দিকে। পরকাললোভী কিছু মানুষ ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করছে দিকে দিকে। আর ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে এত কিছুর পরেও চারিদিকে চলছে ধর্মের জয়জয়কার। ধার্মিক ভালোমানুষের দল তাদের প্রশ্নহীন মন নিয়ে রাতে দিচ্ছে শান্তির ঘুম। কারণ তাদের মন বলছে এতেই মঙ্গল।
.
বিজ্ঞান ও ধর্ম কি সাংঘর্ষিক নয়?
বর্তমানে খুব ফলাও করে ধর্ম-বিজ্ঞানের সমন্বয় কিংবা সম্প্রীতির কথা বলা হলেও বিজ্ঞান এবং ধর্মের দ্বন্দ্ব যুদ্ধের রক্তাক্ত ইতিহাস কারও অজানা নয়। খ্রিস্ট জন্মের পাঁচশ বছর আগে পিথাগোরাস, এনাকু সিমন্ডের মতো অনুসন্ধিৎসু দার্শনিকেরা জানিয়েছিলেন পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহ মাত্র, সূর্যকে ঘিরে অন্য সকল গ্রহের মতো পৃথিবীও ঘুরছে। ধর্মবিরোধী এই মত প্রকাশের জন্য এদের অনেককেই সেসময় সইতে হয়েছিল নির্যাতন। এই ‘কুফরি’ মতবাদকে দুই হাজার বছর পরে পুস্তকাকারে তুলে ধরেছিলেন পোল্যান্ডের নিকোলাস কোপার্নিকাস। বাইবেল- বিরোধী এই সূর্যকেন্দ্রিক তত্ত্ব প্রচারের জন্য কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও আর ব্রুনোর ওপর কী রকমভাবে অত্যাচারের স্টিমরোলার চালানো হয়েছিল সে এক ইতিহাস। ব্রুনোকে তো পুড়িয়েই মারল ঈশ্বরের সুপুত্ররা। তারপরও কি সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘোরা ঠেকানো গেল?
শুধু ব্রুনোই নন, তার সমসাময়িক লুচিলিও ভানিনি, টমাস কিড, ফ্রান্সিস কেট, বার্থেীলোমিউলিগেট সহ অনেককেই ধর্মান্ধদের হাতে নিগৃহীত এবং নির্যাতিত হয়ে নিহত হতে হয়। খ্রিস্টের জন্মের চারশো পঞ্চাশ বছর আগে এনাক্সোগোরাস বলেছিলেন চাঁদের নিজের কোনো আলো নেই। সেই সঙ্গে সঠিকভাবে অনুসন্ধান করেছিলেন চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধি আর চন্দ্রগ্রহণের কারণ এনাক্সোগোরাসের প্রতিটি আবিষ্কারই ছিল ধর্মবাদীদের চোখে জঘন্য রকমের অসত্য। ঈশ্বরবিরোধী, ধর্মবিরোধী আর অসত্য প্রচারের অপরাধে দীর্ঘ আর নিষ্ঠুর নির্যাতনের পর তাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়। ষোড়শ শতকে সুইজারল্যান্ডের বেসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্র এবং ভেষজবিদ্যার অধ্যাপক ফিলিপ্রাস প্যারাসেলসাস ঘোষণা করলেন-মানুষের অসুস্থতার কারণ কোনো পাপের ফল কিংবা অশুভ শক্তি নয়, রোগের কারণ হলো জীবাণু। ওষুধ প্রযোগে জীবাণু নাশ করতে পারলেই রোগ ভালো হয়ে যাবে। প্যারাসেলসাসের এই ‘উদ্ভট তত্ব’ শুনে ধর্মের ধ্বজাধারীরা হা রে রে করে উঠলেন। সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক ধর্মবিরোধী মতবাদ প্রচারের জন্য প্যারাসেলসাসকে হাজির করা হয়েছিল ‘বিচার’ নামক এক প্রহসনের মুখোমুখি। ধর্মান্ধ বিচারকেরা ব্রুনোর মতোই প্যারসেলসাসকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল। প্যারাসেলসাসকে সেদিন জীবন বাঁচাতে মাতৃভূমি ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। অত্যাচার আর নির্যাতন শুধু খ্রিস্টানদের একচেটিয়া ভেবে নিলে ভুল হবে– আজকে মুসলিমরা ইবনে খালিদ, জিরহাম, আল দিমিস্কি, ওমর খৈয়াম, ইবনে সিনা, ইবনে বাজা, আল কিন্দি, আল রাজি কিংবা ইবনে রুশদের মতো দার্শনিকদের জন্য গর্ববোধ করে, কিন্তু সেসব দার্শনিকদের সবাই তাদের সময়ে বৈজ্ঞানিক সত্য কিংবা মুক্তমত প্রকাশের কারণে মৌলবাদীদের হাতে নিগৃহীত, নির্যাতিত কিংবা নিহত হয়েছিলেন।
আজকের দিনের পরিবর্তিত পরিবেশে বিজ্ঞানীদের ওপর এত ঢালাওভাবে অত্যাচার করা কিংবা ডাইনি পোড়ানোর মতো তাদের পুড়িয়ে মারা না গেলেও ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের দল সুযোগ পেলে এখনও বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঠেকাতে মুখিয়ে থাকে। যখনই বিজ্ঞানের কোনো নতুন আবিষ্কার তাদের নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত বিশ্বাসের বিপরীতে যায়, খোদ বিজ্ঞানকে ফেলে দিতে চায আস্তাকুঁড়ে। তাতে অবশ্য লাভ হয় না কিছুই। অযথা গোলমাল বাধিয়ে নিজেরাই বরং সময় সময় হাস্যাস্পদ হন। অধিকাংশ ধার্মিকেরাই এখনও বিবর্তন তত্বকে মন থেকে মেনে নিতে পারেন নি, কারণ ডারউইন প্রদত্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবস্থান ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত সৃষ্টির কল্পকাহিনিগুলোর একশ আশি ডিগ্রী বিপরীতে। এখনও সুযোগ পেলেই ধর্মান্ধ মোল্লার দল প্রগতিশীল দার্শনিক, বিজ্ঞানী কিংবা সাহিত্যিকদেরকে মুরতাদ আখ্যা দেয়, চাপাতি দিয়ে কোপায় কিংবা দেশ থেকে নির্বাসিত করে। এ তো গেল আমাদের মতো দেশগুলোর অবস্থা। তথাকথিত উন্নত বিশ্বে এখনও অশিক্ষিত আর অর্ধশিক্ষিত পাদ্রি আর মোল্লারা উপযাচক সেজে বিজ্ঞানীদের পরামর্শ দিতে আসে বিজ্ঞানীদের কোন গবেষণা নৈতিক আর কোনটা অনৈতিক তা বিবেচনা করে কিংবা দাবি তুলে বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচিতে বিবর্তনের পাশাপাশি ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন কিংবা সৃষ্টিতত্বের গালগপ্পগুলো অন্তর্ভুক্ত করার। কিন্তু এ ধরনের দাবি কতটুকু যৌক্তিক?
২০০৯ সালে মুক্তমনার পক্ষে থেকে একটি ই সংকলনের জন্য লেখা আহ্বান করা হয়েছিল। সংকলনটির শিরোনাম ছিল বিজ্ঞান ও ধর্ম : সংঘাত নাকি সমন্বয়? এই সংকলনের মাধ্যমে বাংলায় বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যকার সম্পর্ক খোঁজা, জানা এবং বোঝার একটি চেষ্টা করা হয়েছে। সন্দেহ নেই, বিজ্ঞান এবং ধর্ম-দুটোর প্রভাব এবং গুরুত্ব আমাদের জীবন এবং সংস্কৃতিতে অপরিসীম। কিন্তু এদের মধ্যে সম্পর্কটি ঠিক কেমন?
অধিকাংশ লেখকই সংকলনটিতে মত দিয়েছেন বিজ্ঞান এবং ধর্মের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে, এবং তা খুব স্পষ্ট। বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টাকে লেখকেরা অর্থহীন এবং বিভ্রান্তিকর বলে রায় দিয়েছেন। তারা যৌক্তিকভাবেই মনে করেন, ধর্মের অনেক প্রাচীন ব্যাখ্যা এবং অভিমতকে বিজ্ঞান যুগে যুগে ভুল প্রমাণ করেছে বহুবার। এর মধ্যে পৃথিবীর বয়সের ভ্রান্ত অনুমান, ভূ-কেন্দ্রিক তত্ব, আত্মার অনুমান, সৃষ্টিতত্ত্বের নানা কেচ্ছা-কাহিনিসহ অনেক কিছুই আছে। এ বিপুল মহাবিশ্বকে ঘড়ির সাথে তুলনা করাকে তারা অতি সরলীকরণ এবং ভ্রান্ত মনে করেন। তারা মনে করেন, আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক তত্বই কোনো কারিগর ছাড়া মহাবিশ্বের অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করতে পারে। মহাবিশ্বের কারিগরের ধারণাকে দার্শনিকভাবেও ভ্রান্ত বলে তারা মনে করেন, কারণ সবকিছুর পেছনে একজন কারিগর থাকলে, সেই কারিগর কোত্থেকে উদ্ভূত হলো সেটাও তো বলতে হবে। তারা আরও মনে করেন, ধর্মগ্রন্থগুলোতে কোনো আধুনিক বিজ্ঞান নেই, বরং আছে আধুনিক বিজ্ঞানের নামে চতুর ব্যাখ্যা এবং গোঁজামিল। সেজন্যই, ধর্মের কাছে বিজ্ঞানকে কখনও দ্বারস্থ হতে হয় না, বরং ধর্মবাদীরাই আজ প্রতিটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পর সেটিকে নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থের সাথে জুড়ে দিতে মুখিয়ে থাকে। কারণ ধর্মবাদীরা জেনে গেছে, ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান ঠিকই টিকে থাকতে পারবে, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান ছাড়া ধর্মগুলোর বেঁচে থাকার আর কোনো উপায় নেই। অধ্যাপক ইরতিশাদ আহমদ তার বিজ্ঞানমনস্ক ধারা ধর্মাচ্ছন্ন স্রোতে’ নামক চমৎকার প্রবন্ধটিতে বলেন[৪৭]–
বিজ্ঞানমনস্ক মানুষেরা বিজ্ঞানকে কখনোই ধর্ম বানাতে চান না, কিন্তু সমন্বয়পন্থী ধর্মাচ্ছন্নরা ধর্মকে সবসময়েই বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাই ধর্ম আর বিজ্ঞানের দ্বন্দ্ব নিয়ে বিজ্ঞানমনস্করা খুব একটা বিচলিত নন, বরং ধর্মাচ্ছন্নদেরই এ নিয়ে বেশি হইচই করতে দেখা যায়। এই দু’এর মধ্যে সমন্বয়ের প্রয়োজনও ধর্মের প্রবক্তারাই অনুভব করেন বেশি। ধর্মবাদীরাই ধর্মকে বিজ্ঞানের প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, বিজ্ঞানমনস্করা নয়। রাসেলের ভাষায়, ‘বিজ্ঞানমনস্ক মানুষেরা মানে না, গুরুত্বপূর্ণ কিংবা কর্তৃত্বসম্পন্ন কেউ বলেছে বলেই কোনোকিছু মেনে নিতে হবে-বরং ঠিক উল্টোটা, সাক্ষ্যপ্রমাণ ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে যা জানা যায় শুধু তাকেই তারা সত্য বলে মেনে নেয়। এই নতুন পদ্ধতির অভূতপূর্ব সাফল্য-তাত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয়বিধ-ধর্মবাদীদের বাধ্য করে ধীরে ধীরে বিজ্ঞানের সাথে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে।
পাশ্চাত্যের ধর্মবেত্তারা বলে বেড়ান আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়েছিল ইউরোপে, খ্রিস্ট ধর্মের হাত ধরে। উদাহরণ হিসেবে দেখান, গ্যালিলিও (মৃত্যু ১৬৪২) ও আইজাক নিউটনের (মৃত্যু ১৭২৭) মতো প্রথম দিককার খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকদের যাঁরা ধার্মিক ছিলেন। অবশ্যই! গ্যালিলিও ও ব্রুনো (মৃত্যু ১৬০০)-র জীবন-কাহিনি আমাদের বর্ণনা করে, ধার্মিক হওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথও তাদের সামনে খোলা ছিল না। তারপরেও তাঁরা ধার্মিকদের রোষানল থেকে রেহাই পেলেন কই?
বিজ্ঞান ও ধর্মের সহস্র বছর ধরা চলা সংঘর্ষের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায় উনিশ শতকে প্রকাশিত দুইটি বই : J.w. Draper-এর History of the Conflictbetween Religion and Science (1873)[৪৮] 978 Andrew Dickson White-এর ‘A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom’ (1896)[৪৯]-এ এরপর থেকেই দীর্ঘদিনের এই প্রাচীনতম সংঘাতের বর্ণনা ধীরে ধীরে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা চলছে[৫০]। বর্তমানে বিজ্ঞান এবং ধর্মের সংঘর্ষ মোচনে বিলিয়ন ডলার খরচ হলেও বিবর্তনের মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে এসে সেই সাম্যাবস্থা একেবারেই মুখ থুবড়ে পড়ে, মনে করিয়ে দেয় প্রাচীন সেই প্রবাদ উলু বনে মুক্তা ছড়ানোর কথা।
আমাদের হাতে সঠিক কোনো পরিসংখ্যান না থাকলেও চারপাশের সমাজ পর্যবেক্ষণ করে বলা যায়, গোঁড়া মুসলমানদের মধ্যে বিবর্তনে বিশ্বাসের হার এক শতাংশও হবে না। সমস্ত মুসলিমপ্রধান দেশগুলোতে হারুন ইয়াহিয়া আর জাকির নায়েকের বিবর্তন সম্বন্ধে ভুল বক্তব্য সম্বলিত সিডি এবং বইয়ের যেভাবে প্রচারণা চলে তা রীতিমতো আতঙ্কজনক। মুসলিম সাহিত্য, মুসলিম অনুষ্ঠান এবং বর্তমান সময়ের আলোচিত মুসলিম স্কলারদের বক্তব্যে বিবর্তন সম্পর্কে মুসলমানদের রায় সহজে অনুধাবন করা যায়। মুসলমানরাও খ্রিস্টান এবং ইহুদিদের মতো বিশ্বাস করে থাকে আদম এবং হাওয়া থেকেই সৃষ্টি হয়েছিল মানব জাতির। বাকি সকল জীবিত প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে এই মানুষদের খেদমত করার জন্য। বিবর্তন নিয়ে আলোচনা নয়, মশা-মাছি বা সমুদ্রের পাদদেশে শিলালিপিতে অবস্থিত এককোষী ব্যাকটেরিয়া সদৃশ ঐমেটালাইটস কেমন করে মানুষের খেদমত করতে পারে সেটা প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রেই মুসলিম স্কলাররা বেশি মনোযোগী। আর সুযোগ পেলেই তারা বিবর্তনবিরোধী বক্তব্যও দিয়ে থাকেন অহরহ। তাদেরই একজনের বক্তব্যের খণ্ডন আমরা দেখতে পাব এই বইয়ের এই সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল, মিঠা নদীর পানি অধ্যায়ে।
খ্রিস্টানদের বিবর্তন সম্পর্কে ধারণা নিয়ে রয়েছে পরিসংখ্যান। ২০০৬ সালের পিউ সার্ভে থেকে জানা যায়, খ্রিস্টান গ্রুপ হোয়াইট ইভানজেলিকানদের ৬৫ ভাগ মনে করে মানুষসহ পৃথিবীর সকল জীবিত প্রাণী বর্তমানে যেমন দেখা যায় ঠিক তেমনভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছিল। অপরদিকে মেইনল্যান্ড প্রটেস্ট্যানসদের মধ্যে ৬২ ভাগ বিবর্তনকে সত্য বলে মনে করে, যাদের মধ্যে মাত্র ৩১ ভাগ প্রাকৃতিক নির্বাচনকে বিবর্তন হওয়ার কারণ হিসেবে দেখে, ২৬ ভাগ মনে করে ঈশ্বর বিবর্তন ঘটিয়েছেন বলে নেওয়া প্রয়োজন, বিবর্তনের কারণ হিসেবে ডারউইন/ ওয়ালেস প্রস্তাবিত প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ব আজকে প্রাণীবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞানসহ অসংখ্য বৈজ্ঞানিক শাখার মূল কাঠামো।
ক্যাথলিক চার্চ ‘অফিসিয়ালি’ বিবর্তনকে সঠিক বলে রায় তারা দিয়েছে। একই সাথে প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্বকেও সঠিক বলে তারা মানে। যদিও মনে করে প্রাকৃতিক নির্বাচনের পেছনে রয়েছে ঈশ্বরের হাত। তারপরও ৩৩ ভাগের মতো ক্যাথলিক মনে করে জীবিত কোনো প্রাণী বিবর্তনের মাধ্যমে আসে নি। ৬৯ ভাগ মনে করে সময়ের সাথে সাথে প্রাণী বিবর্তিত হয়েছে, যাদের মাঝে ২৫ ভাগ কারণ হিসেবে প্রাকৃতিক নির্বাচনকে সত্য বলে মানে। সুতরাং চার্চ যত যাই বলুক না কেন, দেখা যাচ্ছে বিবর্তনকে স্বীকার করে নেওয়ার মতো মানসিক অবস্থায় ক্যাথলিকরা এখনও পৌঁছায় নি।
সংক্ষেপে তিনভাগের একভাগেরও কম আমেরিকান অবিশ্বাস করে বিবর্তন- বিদ্যাকে, যা দিয়ে তাবৎ জীব বিজ্ঞানীরা কাজ করে চলছেন অবিরত।
বিবর্তন এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের সাথে এর বিভিন্ন দ্বন্দ্ব নিয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আরেকটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে মহাবিশ্বের সূচনা সম্বন্ধে। আশা করা যায়, কেন বিজ্ঞান এবং ধর্ম সাংঘর্ষিক সেটার ধারণা পাঠক সেখানে পাবেন।
গত শতাব্দীর অসংখ্য খ্যাতনামা বিজ্ঞানী নিজেদের নাস্তিকতা প্রকাশে দ্বিধা বোধ করেন নিঃ স্টিফেন ওয়াইনবার্গ, স্টিফেন পিনকার, স্টিফেন হকিং, জেমস ওয়াটসন, ফ্রান্সিস ক্রিক, কার্ল ম্যাগান, রিচার্ড ফাইনম্যান, এডওয়ার্ড ও উইলসন, সর্বোপরি আলবার্ট আইনস্টাইন। ১৯৯৮ সালে নেচার পত্রিকার এক প্রবন্ধে এডওয়ার্ড লারসন ন্যাশনাল অ্যাকাডেমি অফ সায়েন্সেস-এর ৫১৭ জন সদস্যের ওপর করা এক জরিপের ফলাফল প্রকাশ করেন। সেখানে দেখা যায়, মাত্র সাত ভাগ সদস্য আব্রাহামিক ঈশ্বরে বিশ্বাসী, ৭২.২ ভাগ অবিশ্বাসী এবং ২০.৮ ভাগ ‘অজ্ঞেযবাদী’! [৫১]
.
বিজ্ঞান এবং ধর্মের ভারসাম্য
অধিকাংশ বিজ্ঞানী ঈশ্বরে অবিশ্বাসী প্রধানত দুইটি কারণে। এক. ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে কোনো প্রমাণ খুঁজে না পাওয়া, দুই. প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ব্যাখ্যায় ঈশ্বরকে বসানোর কোনো প্রয়োজনীয়তা না থাকায়। তারপরও আগের আলোচনা অনুসারে আমরা দেখতে পাই, সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজ্ঞানী, ধর্ম ও বিজ্ঞানকে স্টিফেন গুল্ডের স্বতন্ত্র বলয় হিসেবে দেখতেই বেশি আগ্রহী। এই অবস্থান গ্রহণের ফলে তারা ধর্ম-সংক্রান্ত সকল বিষয় থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করেন। বিজ্ঞানীদের জন্য যেটা সবচেয়ে প্রয়োজনীয়-সেটা হলো, গবেষণা চালিয়ে যাবার ফান্ড বা অর্থ। ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে অর্থাগমের পথকে কণ্টকাকীর্ণ করতে তাদের কেউই আগ্রহী নন। অন্যদিকে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীদের অনেকে মাথার মধ্যে ধর্ম এবং বিজ্ঞানের জন্য দুটি আলাদা কক্ষ তৈরি করে নির্দিষ্ট সময়ে যেকোনো একটিতে অবস্থান করে বাকিটার কথা নির্দ্বিধায় ভুলে যান!
উপরের উদাহরণগুলো একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ে যদি ব্যক্তিটি হয়ে থাকেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের সাবেক অধ্যাপক এবং বর্তমান সাউথ ইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শমসের আলী কিংবা আমেরিকার খ্যাতনামা এবং প্রতিভাবান চিকিৎসাবিজ্ঞানী এবং ‘হিউম্যান জিনোম প্রজেক্টের সাবেক প্রধান ফ্রান্সিস কলিন্সের মতো কেউ।
ইভাঞ্জেলিক খ্রিস্টান ফ্রান্সিস কলিন্স ২০০৬ সালে বিজ্ঞান এবং ধর্মকে একে অন্যের পরিপূরক হিসেবে দেখানোর জন্য লিখেন, ‘ঈশ্বরের ভাষা’ নামে বই[৫২]। একই বিষয় নিয়ে, একদল খ্রিস্টান চিকিৎসকের সামনে উপস্থাপন করা কলিন্সের একটি আলোচনার ভিডিও ইউটিউবের কল্যাণে অনেকেরই দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। বক্তব্যের শুরুতে কলিন্স যখন বিজ্ঞানী হয়েও নিজেকে একজন গর্বিত যিশুখ্রিস্টের অনুসারী বললেন, তখন মুহুর্মুহু করতালিতে তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলেন শ্রোতারা। বক্তব্যের এক পর্যায়ে যখন বিজ্ঞান আলোচনা শুরু হলো এবং কলিন্স যখন বিবর্তনের সত্যতা এবং কেমন করে বিবর্তন ঈশ্বরেরই একটি মহিমা হতে পারে তা বলা শুরু করলেন তখন দেখা গেল মাথা নেড়ে নেড়ে অনেকেই বের হয়ে যাচ্ছেন মিলনায়তন থেকে। ‘নাহ! এনাকে দিয়ে হবে না’–চোখে মুখে এমন একটা অভিব্যক্তিই ছিল বিদায়ী দর্শকদের!
এবার আসা যাক বইয়ের প্রসঙ্গে। বইটিতে কলিন্স তার, ডিএনএ এবং মানব জিন নিয়ে করা গবেষণা বেশ চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন। একই সাথে ধর্মগ্রন্থের সৃষ্টিবাণী এবং এর নতুন রূপ, ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের অসংখ্য ত্রুটিও তিনি আলোচনা করেছেন।
কিন্তু বইয়ের মূল যে লক্ষ্য অর্থাৎ বিশ্বাসের প্রমাণ উপস্থাপন করা–সেটা হয়েছে সামান্য এবং যতটুকুও হয়েছে ততটুকুও স্ববিরোধিতায় পরিপূর্ণ। প্রকৃতিতে থাকা জটিল প্রাণী, বিশেষ করে জটিলতর মানুষ যে বিবর্তনের ফলে উদ্ভব হয়েছে এটা স্বীকার করে কলিন্স বলেছেন, হতে পারে বিবর্তন নামক প্রক্রিয়া দিয়েই ঈশ্বর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। বিবর্তনে ঈশ্বরকে আমদানি করলেও এর যৌক্তিকতা উপস্থাপন করতে পারেন নি কলিন্স। বিবর্তনে ঈশ্বর নামক বহির্জাগতিক শক্তির কোনো ধরনের প্রয়োজনীয়তাই নেই, প্রাকৃতিকভাবেই বিবর্তন কাজ করতে পারে।
বিবর্তনের পর বিগব্যাং নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে কলিন্স বলেন, আমি বুঝি না কেমন করে এমনি এমনি প্রকৃতির সৃষ্টি হতে পারে। কেবল স্থান এবং সময়ের বাইরে অবস্থান করা একজন অতিপ্রাকৃত শক্তিরই সামর্থ্য আছে এই বিপুল মহাবিশ্ব সৃষ্টি করার। কলিন্সের কাছে ‘আমি বুঝি না কেমন করে কথাটি যেন মহাবিশ্ব একজন। ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্টি হয়েছে এমন ধারণার প্রমাণ!!! কেউ কিছু না বুঝে থাকতেই পারেন, কিন্তু তার মানে এই না যে, তিনি না বুঝলেই তার কথা সঠিক! অজ্ঞতাসূচক যুক্তির আরেকটি চমৎকার উদাহরণ এটি।
কলিন্সের মতো বিজ্ঞানীরা সূক্ষা সমন্বয় (Fine Tune) নামক এক ধারণার কথা সুযোগ পেলেই বলেন। তাদের মতে, মহাবিশ্বে বেশ কিছু ধ্রুবকের মান চমৎকারভাবে টিউন করা। একটি ধ্রুবকের মান অন্য কিছু হলেই মহাবিশ্বে জীবনের উৎপত্তি হতো না। এ সিদ্ধান্ত তারা কীভাবে পেলেন? তারা কেমন করে জানলেন, যে ধ্রুবকের মান অন্য রকম হলে ‘অন্য রকম ভাবে প্রাণের উৎপত্তি হতে পারত না?’ বিখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিদ অধ্যাপক ভিক্টর স্টেঙ্গর তার ‘The Unconscious Quantum : Metaphysics in Modern Physics and Cosmology The’ দেখিয়েছেন চলক আর ধ্রুবকগুলোর মান পরিবর্তন করে আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মতোই অসংখ্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তৈরি করা যায়, যেখানে প্রাণের উদ্ভবের মতো পরিবেশের উদ্ভব ঘটতে পারে। এর জন্য কোনো সূক্ষ সমন্বয় বা। ‘ফাইন টিউনিং’-এর কোনো প্রয়োজন নেই[৫৩]। ড. স্টের প্রায়ই বলেন, সূক্ষ-সমন্বয়বাদীদের দাবির এমন কোনো ভিত্তি নেই যাতে তারা অনুমান করতে পারেন যে, একমাত্র একটি সঙ্কীর্ণ সীমা ছাড়া জীবনের উৎপত্তি অসম্ভব। এছাড়াও ‘Physical Review’ জার্নালে সম্প্রতি প্রকাশিত একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধে অ্যান্থনি অ্যাগুরি (Anthony Aguirre) স্বতন্ত্রভাবে দেখিয়েছেন, মহাবিশ্বের ছয়টি প্যারামিটার বা পরিবর্ত রাশিগুলো বিভিন্নভাবে অদলবদল করে গ্রহ, তারা এবং পরিশেষে কোনো একটি গ্রহে বুদ্ধিদীপ্ত জীবন গঠনের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করা সম্ভব-কোনো ধরনের ফাইন টিউনিং কিংবা এনেথ্রাপিক আর্গুমেন্টের প্রয়োগ ছাড়াই[৫৪]।
তারচেয়েও বড় কথা, মহাপরাক্রমশালী, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞানী ঈশ্বর এমন এক মহাবিশ্বই বা কেন সৃষ্টি করলেন যেখানে, পরবর্তীকালে তাকে উল্টা ঘুরে আবার জীবনের উপযোগী করে ফাইন টিউন করতে হলো? তিনি তো চাইলে যেকোনো পরিবেশ এমনকি শূন্যস্থানেও বেঁচে থাকার উপযোগী প্রাণ সৃষ্টি করতে পারতেন। এবং এটাই ধর্মীয় সৃষ্টিতত্বের সবচেয়ে বড় ফাটল। কোনো সুনিপুণ নকশাকারী দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছে বলে মহাবিশ্ব এবং প্রাণ এমন হয়নি। কোনো ধরনের ডিজাইন করা না হলে মহাবিশ্ব এবং প্রাণের যেমন হওয়ার কথা এটি ঠিক তেমনই।
.
বিজ্ঞান কি ঈশ্ববের অস্তিত্ব মিথ্যা প্রমাণ করতে সক্ষম?
পেছনে ফেলে আসা ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়ে কথা বলেছে কেবল দর্শন এবং ধর্মতত্ব। আরও দেখতে পাই, এই পুরোটা সময় জুড়ে বিজ্ঞান সাইড লাইনে বসে শান্ত ছেলের মতো উপভোগ করেছে দার্শনিক এবং ধর্মতাত্বিকদের কথার খেলা। যদিও বিজ্ঞানের বৈপ্লবিক অগ্রগতিতে আজ মানুষের জীবনের প্রায় প্রতিটি দিক আলোকিত, প্রাকৃতিক মহাবিশ্ব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অনেক পরিষ্কার, কিন্তু তারপরও গ্যালারিতে একটি ধ্বনি এখনও উচ্চারিত হয় : ঈশ্বর সম্পর্কে বিজ্ঞানের কিছু বলার অধিকার আমাদের নেই। ঈশ্বর, যিনি কিনা সকল বাস্তবতার উৎস, বাস্তবতার ব্যাখ্যাকারী-বিজ্ঞানের অধিকার নেই, তার সম্পর্কে কথা বলার!
‘রক অফ এজেস’ নামে ২০০৩-এ প্রকাশিত বইয়ে, বিখ্যাত প্রত্নতাত্বিক স্টিফেন জে. গুল্ড কর্তৃক ধর্ম এবং বিজ্ঞানকে স্বতন্ত্র বলয় হিসেবে ভাবার প্রস্তাবনা এই অধ্যায়ের শুরুতেই আমরা জেনেছি। জে. গুল্ড বিজ্ঞানকে প্রকৃতি ব্যাখ্যা করার হাতিয়ার আর ধর্মকে নৈতিকতার দর্শন হিসেবে অভিহিত করার মাধ্যমে কর্মক্ষেত্র আলাদা করে সংঘর্ষ এড়াতে চেয়েছেন। কিন্তু তার প্রস্তাবনা মহান হলেও বিজ্ঞান এবং ধর্মের কর্মক্ষেত্র বণ্টন ত্রুটিময়। ধরা যাক, ইসলাম ধর্ম মানুষের নৈতিকতা বিষয়ে দিক-নির্দেশনা প্রদান করে। কিন্তু একই সাথে অসুখ হলে অনেক মুসলমান মসজিদের হুজুরের কাছে যান, পানি-পড়া গ্রহণ করতে। যেখানে এক গ্লাস পানিতে কিছু দোয়া পড়ে হুজুররা ফুঁ দিয়ে দেন। ইসলামে বিশ্বাসীদের মতে এই পানি পড়া রোগীর রোগ দূর করতে সক্ষম। এখন ভেবে দেখুন তো এখানে কি বিজ্ঞানের কিছুই করার নেই? আছে। বিজ্ঞান এই পানি পড়ার রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে দেখাতে সক্ষম–ঐশ্বরিক এই পানি পড়াতে আসলেই কোনো রোগ-ব্যাধি সারানোর নিয়ামক আছে, নাকি এটি শুধুই পানি! একই সাথে নৈতিকতা-যার ফলাফল/পরিমাণ পর্যবেক্ষণযোগ্য, যার উৎপত্তি হয়েছে প্রাকৃতিক কারণে সেটি নিয়েও বিজ্ঞান কেন কথা বলতে পারবে না? পারবে এবং নৈতিকতার প্রকৃতি গবেষণায় বিজ্ঞান ইতোমধ্যে অনেক দূর পথ পাড়িও দিয়ে ফেলেছে।
ধর্মবেত্তারা বিজ্ঞানের ঈশ্বর আলোচনার সমালোচনা করলেও, নিজেরা ঠিকই সেই খ্রিস্টপূর্ব ৭৭ সাল থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিজ্ঞানময় যুক্তি প্রদান করে চলছেন। ইসলামি বিশ্বে ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা, ভারতীয় ধর্মব্যবসায়ী জাকির নায়েক তার অসংখ্য লেকচারে বিজ্ঞানের আলোকে আল্লাহর অস্তিত্ব প্রমাণ করেছেন। এছাড়াও আল্লাহ প্রদত্ত ঐশী গ্রন্থ কোরআন শরীফকেও বিজ্ঞানময় করার চেষ্টা চলছে শত বছর ধরে।
ছবি। পেজ ৬৬।
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের লাইব্রেরি ঘাঁটলেই কোরআন এবং বিজ্ঞান, বিজ্ঞানময় কোরআনের মতো অসংখ্য বইয়ের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। একথা শুধু ইসলামের জন্য প্রযোজ্য না, প্রযোজ্য সকল ধর্মের ক্ষেত্রেই। সরাসরি ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রমাণ করার চেয়ে তার প্রেরিত গ্রন্থকে বিজ্ঞানময় প্রমাণ করাকেই অপেক্ষাকৃত সহজ বলেই মনে করে থাকেন ধর্মতত্ত্ববিদরা। গ্রন্থ বিজ্ঞানময় প্রমাণ হলেই, প্রমাণ হবে ঈশ্বর আছেন যিনি কিনা হাজার বছর আগেই বর্ণনা করে গেছেন বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক আবিষ্কৃত নানা বিষয়। খ্রিস্টান ধর্মকে বিজ্ঞানময় প্রমাণ করার জন্য ১৯৪৭ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করা হয় টেম্পলিটন ফাউন্ডেশন। এখন পর্যন্ত কয়েক বিলিয়ন ডলার খরচ করা এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিবছর ধর্মীয় বিজ্ঞানের গবেষণার জন্য ৬০ মিলিয়ন ডলার বৃত্তি প্রদান করা হয় দেখা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, ধর্ম নিজেদের বিজ্ঞানময় করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে অবিরত, কিন্তু বিজ্ঞানের অধিকার নেই ধর্মের উৎস, ঈশ্বর নিয়ে কথা বলার!
এই বইয়ের পরবর্তী দুই অধ্যায়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বের বিজ্ঞানময় আলোচনা আমরা করব। আমরা দেখাব যে, বিজ্ঞান এখন এতটাই উন্নত যে এর মাধ্যমে আমরা ইহুদি-খ্রিস্টান-মুসলিমদের পূজনীয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব,অনস্তিত্ব সম্পর্কে যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারি। একটি বিষয় উল্লেখ্য, এই ইহুদি-খ্রিস্টান মুসলমানদের ঈশ্বর কাগজে কলমে সংজ্ঞায়িত হলেও পরস্পরবিরোধিতা থেকে মুক্ত নয়। একই ঈশ্বরের পূজারী হলেও, এই তিনটি ধর্মের মধ্যে ঈশ্বরের সংজ্ঞা নিয়ে মতপার্থক্য আছে। পার্থক্য রয়েছে একই ধর্মের বিভিন্ন শাখার মধ্যেও সংঘাত রয়েছে, সাধারণ ধার্মিক এবং ধর্মতত্ত্ববিদদের মধ্যেও আমরা তাই চেষ্টা করেছি ঈশ্বরের সর্বজনস্বীকৃত কিছু গুণাবলির ওপরেই। যেমন : মানুষের সৃষ্টি, মহাবিশ্বের সৃষ্টি ইত্যাদি।
উপরে উল্লেখিত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় তিনটি ধর্মে ঈশ্বরকে দেখা হয় পদার্থ, স্থান এবং কালোত্তীর্ণ একজন অতি পরাক্রমশালী সত্ত্বা হিসেবে-যদিও তার সকল কর্মকাণ্ডই সম্য-স্থান, কাল এবং পদার্থকে ঘিরে। এই ঈশ্বর ডেইজম বা প্রত্যাদেশ-বিরোধী ঈশ্বর, যিনি কিনা মহাজাগতিক কোনোকিছুতেই হস্তক্ষেপ করেন না, প্রার্থনা শোনেন না এমন ঈশ্বর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, সম্পূর্ণ আলাদা প্যান্থিয়েজম বা সর্বেশ্বরবাদে (প্রতিটি সত্ত্বাই ঈশ্বর) বিশ্বাসীদের ঈশ্বর থেকে।
সুতরাং এই বইয়ের পরবর্তীকালে যতবারই ঈশ্বর শব্দটি উল্লেখ করা হবে, ততবারই আমরা বোঝাব পৃথিবীর একেশ্বরবাদী সবচেয়ে বড় তিনটি ধর্মের ঈশ্বরের কথা। যিনি পৃথিবীর প্রতিটি ন্যানো মিটারে, ন্যানো সেকেন্ড থেকে ন্যানো সেকেন্ডে ঘটা সকল ঘটনা থেকে শুরু করে অতিদূরবর্তী গ্যালাক্সিতে আণবিক নিউক্লীতে কোয়ার্ক কণার ক্ষীণ আন্তক্রিয়ার ফলে তারা সৃষ্টির নিয়ন্ত্রক। একই সাথে তিনি তার সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ থেকে শুরু করে সৃষ্টির অ-সেরা জীব পর্যন্ত সবার প্রতি সেকেন্ডের চিন্তা সম্পর্কে অবগত থাকেন, শুধু তাই না তিনি প্রার্থনা শুনেন এবং তার দলের লোকদের জয়ে নিশ্চিত ভূমিকা রাখেন।
০২. এই সুন্দর ফুল, সুন্দর ফুল কিংবা মিঠা নদীর পানি
মানুষের উৎপত্তি সম্পর্কে দুটি তত্ব রয়েছে : অবৈজ্ঞানিক অধঃপতনতত্ব, বৈজ্ঞানিক বিবর্তন তত্ব। অধঃপতনতত্ত্বের সারকথা মানুষ স্বর্গ থেকে অধঃপতিত। বিবর্তনতত্ত্বের সারকথা মানুষ বিবর্তনের উৎকর্ষের ফল। অধঃপতনবাদীরা অধঃপতনতত্বে বিশ্বাস করে; আমি যেহেতু মানুষের উৎকর্ষে বিশ্বাস করি, তাই বিশ্বাস করি বিবর্তনতত্বে। অধঃপতনের থেকে উৎকর্ষ সব সময়ই উৎকৃষ্ট।
–হুমায়ুন আজাদ
প্যালের ঘড়ি
এই সুন্দর ফুল, সুন্দর ফল কিংবা মিঠা নদীর পানিতে নাম না জানা হরেক রকমের মাছ-সবকিছু কী চমৎকার। এত সুন্দর, এত জটিল প্রাণিজগতের দিকে তাকালে বোঝা যায় এগুলো এমনি এমনি আসে নি। এদের এভাবেই নিখুঁতভাবে তৈরি করা হয়েছে। ঈশ্বরের অস্তিত্বের সপক্ষে সন্দেহাতীতভাবে এটিই সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত যুক্তি। বিভিন্ন ভাষায়, বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হলেও যুক্তির মূল কাঠামো একই[৫৫]।
প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্ব খোঁজার দীর্ঘ ইতিহাসের সূচনা গ্রিকদের দ্বারা[৫৬] হলেও বিষয়টিকে জনপ্রিয় করার পেছনে সবচেয়ে বেশি অবদান ধর্মবেত্তা ও দার্শনিক উইলিয়াম প্যালের (১৭৪৩-১৮০৫)। প্যালে জ্যোতির্বিজ্ঞান দিয়ে তার চিন্তাভাবনা শুরু করলেও খুব দ্রুত বুঝে গিয়েছিলেন, বুদ্ধিদীপ্ত স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞান উপযুক্ত মাধ্যম নয়[৫৭]। তার কাছে উপযুক্ত মাধ্যম মনে হয়েছিল জীববিজ্ঞানকে। নিজের ভাবনাকে গুছিয়ে সৃষ্টির পরিকল্প যুক্তি বা ‘ডিজাইন আর্গুমেন্ট’ নিয়ে তিনি ১৮০২ সালে প্রকাশ করেন। ‘Natural Theology, or Evidence of Existence and Attributes of the Deity, collected from the Appearances of Nature’ নামের বইটি[৫৮]। ধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত এই বিখ্যাত বইয়ে প্যালে রাস্তার ধারে একটি ঘড়ি এবং পাথর পড়ে থাকার উদাহরণ দেন। তিনি বলেন–
ধরা যাক, ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে হঠাৎ আমার পা একটা পাথরে লেগে গেল। আমি নিজেকে প্রশ্ন করলাম, এই পাথরটা কোত্থেকে এলো? আমার মনে উত্তর আসবে-প্রকৃতির অন্য অনেক কিছুর মতো পাথরটাও হয়ত সবসময়ই এখানে ছিল। …কিন্তু ধরা যাক, আমি পথ চলতে গিয়ে একটা ঘড়ি কুড়িয়ে পেলাম। এবার কিন্তু আমার কখনোই মনে হবে না যে ঘড়িটিও সব সময়ই এখানে পড়ে ছিল।
নিঃসন্দেহে ঘড়ির গঠন পাথরের মতো সরল নয়। একটি ঘড়ি দেখলে বোঝা যায়-ঘড়ির ভেতরের বিভিন্ন ছোট ছোট অংশগুলো কোনো এক কারিগর এমনভাবে তৈরি করেছেন যেন সেগুলো সঠিকভাবে সমন্বিত হয়ে কাঁটাগুলোকে ডায়ালের চারপাশে মাপমতো ঘুরিয়ে ঠিকঠাক মতো সময়ের হিসাব রাখতে পারে। কাজেই পথে ঘড়ি কুড়িয়ে পেলে যে কেউ ভাবতে বাধ্য যে ওখানে আপনা আপনি ঘড়ির জন্ম হয় নি বরং এর পেছনে একজন কারিগর রয়েছেন যিনি অতি যত্ন করে একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ঘড়িটি তৈরি করেছেন। একই যুক্তিমালার পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে প্যালে বেছে নিয়েছিলেন আমাদের জীবদেহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ চোখকে। চোখকে প্যালে ঘড়ির মতোই এক ধরনের জটিল যন্ত্র হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন, কারণ তার মতে, ‘ঘড়ির মতোই এটি (চোখ) বহু ছোট-খাটো গতিশীল কলক সমন্বিত এক ধরনের জটিল যন্ত্র হিসেবে আমাদের কাছে আবির্ভূত হয়, যেগুলোর প্রত্যেকটি একসাথে কাজ করে অঙ্গটিকে কর্মক্ষম করে তুলে।
পূর্ববর্তী অন্যান্য প্রাকৃতিক ধর্মবেত্তার মতো প্যালেও জীবজগতকে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে জীবের অভিযোজনের ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্যালে লক্ষ্য করেছিলেন যে, প্রতিটি জীবদেহে নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য নির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে, যা জীবটিকে একটি নির্দিষ্ট পরিবেশে টিকে থাকতে সহায়তা করে। তিনি জটিল জীবদেহকে কিংবা চোখের মতো প্রত্যঙ্গকে ঘড়ির কাঠামোর সাথে তুলনা করার মাধ্যমে দেখাতে চেয়েছিলেন স্রষ্টার সুমহান পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য আর নিপুণ তুলির আঁচড়।
প্যালের এই যুক্তির নাম সৃষ্টির পরিকল্প যুক্তি বা ‘ডিজাইন আর্গুমেন্ট’ দুইশ বছর পেরিয়ে গেলেও এই যুক্তি আজও সকল ধর্মানুরাগীরা নিজ নিজ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণে ব্যবহার করে থাকেন। কয়েক সপ্তাহ আগেই ঈশ্বর আছে কী নেই এই আলোচনায় আমার এক বন্ধু আর সহ্য করতে না পেরে উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে এক মিনিটের জন্য তার কথা শুনতে অনুরোধ করল। এক যুক্তিতেই সকল সন্দেহকে কবর খুঁড়ে দেওয়ার অভিপ্রায়ে সে শুরু করল–ধর যে, তুই রাস্তা দিয়ে হাঁটছিস, হঠাৎ দেখলি তোর সামনে একটি পাথর আর ঘড়ি পড়ে আছে … প্যালের ঘড়ির মৃত্যু নাই।
জীবজগতের জটিলতা নিয়ে অতি-চিন্তিত সৃষ্টিবাদীরা জটিলতার ব্যাখ্যা হিসেবে আমদানি করেছেন ঈশ্বরকে। ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন–সুতরাং সবকিছু ব্যাখ্যা হয়ে গেছে বলে হাত ঝেড়ে ফেললেও তাদের তত্ব তৈরি করে যায় আরও মহান এক জটিলতা। তর্কের স্বার্থে যদি ধরে নেই, সবকিছু এতটাই জটিল যে, বাইরের কারও সহায়তা ছাড়া এমন হওয়া সম্ভব নয়, তাহলে তো এর সৃষ্টিকর্তাকে আরও হাজারগুণ জটিল হতে হবে। তিনি তবে কীভাবে সৃষ্টি হলেন? প্যালের ঘড়ি ছাড়াও লেগো সেটের মাধ্যমে একই যুক্তি উপস্থাপন করা হয়। ধরা যাক, লেগো সেট দিয়ে তৈরি করা হলো একটি গ্রিনলাইন স্ক্যানিয়া মডেলের বাস। একজন দেখেই বুঝবে, বুদ্ধিমান মানুষ লেগো সেটের মাধ্যমে বাসটি তৈরি করেছে। এখন কেউ যদি বাসের লেগোগুলো আলাদা করে একটি বস্তায় ভরে ঝাঁকাতে থাকে তাহলে কী আদৌ কোনোদিন বস্তা থেকে আরেকটি বাস বের হয়ে আসবে? আসবে না।
উপরি-উক্ত উদাহরণে সৃষ্টিবাদীরা বাস তৈরির দুটি প্রক্রিয়ার ‘ধারণা’ দেন আমাদের, একটি বুদ্ধিমান কোনো সম্বার হস্তক্ষেপ দ্বারা (যার অস্তিত্বের উৎস নিয়ে সৃষ্টিবাদীরা মোটেই চিন্তিত নন, যতটা চিন্তিত ঘড়ি নির্মাণ কিংবা লেগোর বাস নিয়ে), আরেকটি বস্তায় ভরে ঝাঁকি দেওয়া। কিন্তু বস্তায় ভরে ঝাঁকি দেওয়ার ধারণার বদলে আমাদের হাতে প্রাণিজগতের জটিলতা ব্যাখ্যা করার জন্য স্বয়ংসম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক তত্ব রয়েছে, শত সহস্র পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যেই তত্ত্বের সত্যতা নিশ্চিত করা হয়েছে, যেটি সকল প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে খাপ খায়। এই তত্ত্বের নাম ডারউইনের বিবর্তন তত্ব।
.
বিবর্তন তত্ব
১৮২৭ সালে চার্লস ডারউইন (মৃত্যু : ১৮৪২) যখন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে পড়াশোনা করার জন্য, তখন তাঁকে বরাদ্দ করা হয় ৭০ বছর আগে প্যালে যে কক্ষে থাকতেন সেই কক্ষটিই[৫৯]। ধর্মতত্ত্বের সিলেবাসে ততদিনে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়া প্যালের কাজে গভীরভাবে আলোড়িত ডারউইন পরবর্তীকালে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘ইউক্লিডের রচনা আমাকে যেরকম মুগ্ধ করেছিল ঠিক সেরকম মুগ্ধ করেছিল প্যালের বই। কিন্তু পরবর্তীকালে এই ডারউইনই প্যালের প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক জবাব দানের মাধ্যমে এই যুক্তিকে সমাধিস্থ করেন।
প্রাণিজগতে বিবর্তন হচ্ছে, এই ব্যাপারটি প্রথম ডারউইন উপলব্ধি করেন নি। তৎকালীন অনেকের মধ্যেই ধারণাটি ছিল, তার মধ্যে ডারউইনের দাদা ইরাসমাস ডারউইন অন্যতম[৬০]। এপাশ ওপাশে ধারণা থাকলেও, বিবর্তন কেন ঘটছে আর কীভাবে ঘটছে, এই প্রশ্নে এসেই আটকে গিয়েছিলেন তাদের সবাই। ১৮৫৯ সালে ডারউইন তার বই ‘অরিজিন অফ স্পিশিজ’ প্রকাশ করেন[৬১]। ৪৯০ পাতার এই বইয়ে ডারউইন উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে ব্যাখ্যা করেন বিবর্তন কী, বিবর্তন কেন হয়, কীভাবে, প্রাণিজগতে বিবর্তনের ভূমিকাই বা কী। এই বইয়ে বিবর্তন নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার ইচ্ছে আমাদের নেই। কিন্তু সৃষ্টিবাদী বা ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন প্রবক্তাদের ভুল-ত্রুটি ব্যাখ্যা ও তাদের বক্তব্যের অসাড়তা সর্বোপরি প্রাণীর প্রাণী হওয়ার পেছনে ঈশ্বরের হাতের ভূমিকা প্রমাণের আগে পাঠকদের বিবর্তন তত্ত্বের সাথে সংক্ষিপ্ত পরিচয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছি।
প্রথমেই দেখে নেওয়া যাক বিবর্তন কাকে বলে এবং এটি কীভাবে ঘটে।
বিবর্তন : বিবর্তন মানে পরিবর্তনসহ উদ্ভব। সময়ের সাথে সাথে জীবকুলের মাঝে (জনপুঞ্জে) পরিবর্তন আসে। প্রকৃতির বর্তমান অবস্থা, জীবাশ্মের রেকর্ড, জেনেটিক্স, আণবিক জীববিজ্ঞানের মতো বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার গবেষণা থেকে এটি স্পষ্ট বোঝা গেছে। গাছ থেকে আপেল পড়ার মতোই বিবর্তন বাস্তব-এ নিয়ে আর কোনো সন্দেহ নেই।
বৈচিত্রময় বংশধবের উৎপত্তি : সাধারণ একটি পূর্বপুরুষ থেকে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বিস্তারের মাধ্যমে বিবর্তন ঘটে। প্রতিটি শাখা-প্রশাখার জীব তার পূর্বপুরুষ থেকে খানিকটা ভিন্ন হয়। মনে রাখা প্রয়োজন বংশধরেরা কথনও হুবহু তাদের পিতামাতার অনুরূপ হয় না, প্রত্যেকের মাঝেই খানিকটা বৈচিত্র্য তথা ভ্যারিয়েশন বা প্রকরণ তৈরি হয়। আর এই বৈচিত্র্যের কারণেই সদা পরিবর্তনশীল পরিবেশে অভিযোজন নামক প্রক্রিয়াটি কাজ করতে পারে। অসংখ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে পরিবেশে সবচেয়ে উপযোগীরাই টিকে থাকে।
ধীর পরিবর্তন : পরিবর্তন সাধারণত খুব ধীর একটি প্রক্রিয়া। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে বিবর্তনের মাধ্যমেই নতুন প্রজাতির জন্ম হতে পারে।
প্রজাতির ক্রমবর্ধন : এক প্রজাতি থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে অনেক নতুন প্রজাতির উদ্ভব ঘটতে পারে। সে কারণেই আজকে আমরা প্রকৃতিতে এত কোটি কোটি প্রজাতির জীব দেখতে পাই। আবার অন্যদিকে যারা সদা পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিকতার সাথে টিকে থাকতে অক্ষম তারা বিলুপ্ত হয়ে যায়। প্রকৃতিতে প্রায় ৯০-৯৫% জীবই বিলুপ্ত হয়ে গেছে।
প্রাকৃতিক নির্বাচন : চার্লস ডারউইন এবং আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস স্বাধীনভাবে বিবর্তনের যে প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছিলেন তা এভাবে কাজ করে :
ক) জনসংখ্যা সর্বদা জ্যামিতিক অনুপাতে বৃদ্ধি পায়।
খ) জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকলেও একটি প্রাকৃতিক পরিবেশে জনসংখ্যা সবসময় নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকে।
গ) পরিবেশে একটি ‘অস্তিত্বের সংগ্রাম থাকে। ফলে উৎপাদিত সকল জীবের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না।
ঘ) প্রতিটি প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে বৈচিত্র্য তথা ভ্যারিয়েশন আছে।
ঙ) অস্তিত্বের নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চলার সময় যে প্রজাতির সদস্যদের মাঝে পরিবেশে টিকে থাকার জন্য অধিক উপযোগী বৈশিষ্ট্য আছে তারাই সর্বোচ্চ সংখ্যক বংশধর রেখে যেতে পারে। আর যাদের মাঝে পরিবেশ উপযোগী বৈশিষ্ট্য কম তাদের বংশধরও কম হয়, যার ফলে এক সময় তারা বিলুপ্তও হয়ে যেতে পারে। বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এই প্রক্রিয়াটিকেই বলা হয় ‘প্রভেদক প্রজননগত সাফল্য[৬২]।
শেষ পয়েন্টটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং এর মাধ্যমে ঘটা বিবর্তনীয় পরিবর্তন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে ঘটে। সেই নির্দিষ্ট পরিবেশে প্রজাতির সদস্যরা কে সবচেয়ে বেশি বংশধর রেখে যাতে পারে, তথা কে সবচেয়ে সফলভাবে নিজের জিনকে পরবর্তী প্রজন্মে প্রবাহিত করতে পারে, তার ওপর বিবর্তনের প্রক্রিয়া নির্ভর করে। বিবর্তনের কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই, প্রজাতির প্রগতি কোনদিকে হবে, বা এর মাধ্যমে আদৌ কোনো কৌশলগত লক্ষ্য অর্জিত হবে কিনা এ সম্পর্কে প্রাকৃতিক নির্বাচনের কিছুই বলার নেই। এমনকি বিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের উৎপত্তি হতেই হবে বা বুদ্ধিমত্তা নামক কোনোকিছুর বিবর্তন ঘটতেই হবে এমন কোনো কথাও নেই। বিবর্তন কোনো সিঁড়ি বেয়ে উপরের দিকে ওঠে না, বা কোনো পিরামিডের চূড়ায় উঠতে চায় না এমন ভাবার কোনোই কারণ নেই যে, মানুষ তৈরির লক্ষ্য নিয়ে এতকাল ধরে প্রাকৃতিক নির্বাচন কাজ করেছে। বরং বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্ট অসংখ্য লক্ষ্যহীন শাখা-প্রশাখারই একটিতে মানুষের অবস্থান। তাই নিজেদের সৃষ্টির সেরা জীব বলে যে পৌরাণিক ধারণা আমাদের ছিল সেটারও কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। কারণ সেরা বলে কিছু নেই। সব প্রাণীরই কিছু না কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, যার নিরিখে মনে হতে পারে যে তারা হতো সেরা বা অনন্য। যেমন, বাদুড়ের আল্টাসনিক বা অতিশব্দ তৈরি করে শিকার ধরার এবং পথ চলার ক্ষমতা আছে, যা অনেক প্রাণীরই নেই। মৌমাছির আবার পোলারাইজড বা সমবর্তিত আলোতে দেখার বিরল ক্ষমতা আছে, যা আমাদের নেই। মানুষের ক্ষেত্রে যে বৈশিষ্ট্যটি অনন্য তা হল– মানুষ খুব উন্নত মস্তিষ্কের অধিকারী, যেটা হয়ত টিকে থাকার জন্য আমাদের বাড়তি সুবিধা দিচ্ছে। আর মানুষের এত উন্নতির পেছনেও মূল কারণ কিন্তু প্রভেদক প্রজননগত সাফল্য। আমরা অনেক বংশধরের জন্ম দিতে পারি, এমনকি তারা পূর্ণবয়স্ক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের ভরণপোষণও করতে পারি। অবশ্য একই বৈশিষ্ট্যে উল্টো জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আবার আমাদের বিলুপ্তও করে দিতে পারি।
.
বিবর্তন শুধুই একটি তত্ব নয়
বিবর্তনকে উদ্দেশ্য করে সৃষ্টিবাদীদের সবচেয়ে প্রচারিত সন্দেহ, বিবর্তন শুধুই একটি তত্ব, এর কোনো বাস্তবতা নেই। সত্যিই কি তাই? বিজ্ঞানীরা বাস্তবে ঘটে না, এমন কোনোকিছু নিয়ে কথনও তত্ব প্রদান করেন না। বাস্তবতা কাকে বলে? কোনো পর্যবেক্ষণ যখন বারবার বিভিন্নভাবে প্রমাণিত হয় তখন তাকে আমরা বাস্তবতা বা সত্য (fact) বলে ধরে নেই।
প্রাণের বিবর্তন ঘটছে। প্রতিটি প্রজাতি স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্টি করা হয় নি, বরং প্রাণের উদ্ভবের পর থেকে প্রতিনিয়ত পরিবেশের বিভিন্ন প্রভাবের কারণে এক প্রজাতি বিবর্তিত হয়ে অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এপ (Ape)-রা রাতে ঘুমালো, সকালে উঠে দেখলো তারা সবাই হোমোসেপিয়েন্সে রূপান্তরিত হয়ে গেছে-এমন না, এটি লক্ষ বছরে পরিবেশে টিকে থাকার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্তনের ফসল। প্রতি এক রূপ থেকে আরেক রূপে বিবর্তিত হতে পারে না, এটা এই যুগে এসে মনে করাটা পাপ, যখন দেখা যায়, চৈনিকরা যোগাযোগ খরচ কমানোর জন্য গোল তরমুজকে চারকোণা করে ফেলেছে। কবুতর, কুকুরের ব্রিডিং সম্পর্কেও আমরা সবাই অবগত। মাত্র কয়েক প্রজন্মেই এক প্রজাতির কুকুর থেকে আরেক প্রজাতির উদ্ভব হয়, সেখানে পরিবেশ পেয়েছে লক্ষ-কোটি বছর। ‘হোয়াই ইভোলিউশন ইজ টু’ বইটিতে প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী এবং সুলেখক জেরি কোয়েন বলেন–
প্রতিদিন, কয়েকশত পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশিত হয় … এবং এদের প্রতিটি বিবর্তনের সত্যতা নিশ্চিত করে। খুঁজে পাওয়া প্রতিটি জীবাশ্ম, সিকোয়েন্সকৃত প্রতিটি ডিএনএ প্রমাণ করে একটি সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে প্রতিটি প্রজাতির উৎপত্তি হয়েছে। প্রাক-ক্যামব্রিয়ান শিলায় আমরা স্তন্যপায়ী কোনো প্রাণীর জীবাশ্ম পাই নি, পাই নি পাললিক শিলার একই স্তরে মানুষ এবং ডাইনোসরের জীবাশ্ম। লক্ষাধিক সম্ভাব্য কারণে বিবর্তন ভুল প্রমাণিত হতে পারত, কিন্তু হয় নি-প্রতিটি পরীক্ষায় সে সাফল্যের সাথে প্রমাণিত হয়েছে।
সুতরাং আমাদের পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে আমরা অনুধাবন করতে পারি, বিবর্তন একটি বাস্তবতা। এখন পর্যবেক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করার জন্যই প্রয়োজন হয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের। যেমন গাছ থেকে আপেল পড়ে, এটি একটি বাস্তবতা, একে ব্যাখ্যা করা হয় নিউটনের মহাকর্ষ তত্ব দ্বারা। তত্ব কোনো সাধারণ বাক্য নয়, বাস্তবতা ব্যাখ্যা করার জন্য বিজ্ঞানীরা প্রথমে একটি হাইপোথিসিস স্থির করান। পরবর্তীকালে এই হাইপোথিসিসকে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সূত্রের মাধ্যমে আঘাত করা হয়। যদি যৌক্তিকভাবে একটি হাইপোথিসিস শেষ পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ প্রমাণ একে সমর্থন করে তখন একে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ব উপাধি দেওয়া হয়। বিবর্তনকে যে তত্ব দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়, তার নাম ‘প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ব’।
প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব নিয়ে ডারউইন একদিকে যেমন নিঃসংশয় ছিলেন অপরদিকে ছিলেন দ্বিধাগ্রস্ত। কারণ লক্ষ-কোটি প্রজাতির মধ্যে যে কোনো একটি প্রজাতি এই তত্ত্ব অনুসরণ করে উদ্ভূত না হলেই তত্বটিকে বাতিল করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিলো। দীর্ঘ বিশ বছর বিভিন্ন প্রমাণ সংগ্রহ করে তবেই ডারউইন ১৮৫৮ সালে তত্বটি প্রকাশ করেন[৬৩]। তারপর থেকেই বিবর্তনবাদ বিজ্ঞানীদের ছুরির তলে বাস করতে থাকে। গত দেড়শ বছর ধরে বিভিন্নভাবে বিবর্তন তত্বকে পরীক্ষা করা হয়েছে, এটি কখনোই ভুল প্রমাণিত হয় নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, প্রতিটা নতুন ফসিল আবিষ্কার বিবর্তন তত্বের জন্য একটি পরীক্ষা। একটি ফসিলও যদি বিবর্তনের ধারার বাইরে পাওয়া যায় সেই মাত্র তত্বটি ভুল বলে প্রমাণিত হবে। একবার বিজ্ঞানী জেবি এস হালডেনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কীভাবে বিবর্তনকে ভুল প্রমাণ করা যায়? উত্তরে হালডেন বলেছিলেন—[৬৪]
কেউ যদি প্রাক-ক্যামব্রিয়ান যুগে খরগোশের ফসিল খুঁজে পায়।
বলা বাহুল্য এধরনের কোনো ফসিলই এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি। না হওয়ারই কথা, কারণ বিজ্ঞানীরা বিবর্তনের যে ধারাটি আমাদের দিয়েছেন তা হলো :
মাছ → উভচর → সরীসৃপ → স্তন্যপায়ী প্রাণী।
খরগোশ যেহেতু একটি পুরোপুরি স্তন্যপায়ী প্রাণী, সেহেতু সেটি বিবর্তিত হয়েছে অনেক পরে এবং বিভিন্ন ধাপে (মাছ থেকে উভচর, উভচর থেকে সরীসৃপ এবং সরীসৃপ থেকে শেষ পর্যন্ত খরগোশ), তাই এর জন্য সময় লেগেছে। বিস্তর। প্রাক-ক্যামব্রিয়ান যুগে খরগোশের ফসিল পাওয়ার কথা নয়, কারণ বিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী এ সময় (প্রাক-ক্যামব্রিয়ান যুগে) থাকার কথা কতকগুলো আদিম সরল প্রাণ-যেমন সায়নোব্যাকটেরিয়া (ফসিল রেকর্ডও তাই বলছে)। আর স্তন্যপায়ী প্রাণীর উদ্ভব ঘটেছে ট্রায়োসিক যুগে (প্রাক-ক্যামব্রিয়ান যুগ শেষ হওয়ার ৩০ কোটি বছর পরে)। কাজেই কেউ সেই প্রাক-ক্যামব্রিয়ান যুগে খরগোশের ফসিল খুঁজে পেলে তা সাথে সাথেই বিবর্তন তত্বকে নস্যাৎ করার জন্য যথেষ্ট হতো।
তত্ত্বের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অনুমান করা। যার মাধ্যমে এটিকে ভুল প্রমাণের সুযোগ থাকে। আধুনিক পিঁপড়াদের পূর্বপুরুষের ফসিল কোথা থেকে পাওয়া যাবে সেটা বিবর্তন তত্ব দিয়ে অনুমান করে সত্যতা যাচাই করা হয়েছে। ডারউইন নিজেই বলে গিয়েছিলেন, মানুষের পূর্বপুরুষের জীবাশ্মের সন্ধান মিলবে আফ্রিকায় এবং জীবাশ্মবিজ্ঞানীরা সন্ধান পেয়েছেন এমন অনেক জীবাশ্মের। এ ধরণের অনুমান যদি ভুল হতো তাহলে আমরা নিমেষেই বিবর্তনকে বাতিল করে দিতে পারতাম, কিন্তু হয় নি। মুক্তমনার বিবর্তন আর্কাইভে এই তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ বহু অনুমানের তালিকা পাওয়া যাবে[৬৫]।
তবে এতসব কিছুর মধ্যে আমাদের প্রিয় একটি উদাহরণ দেই। ডারউইনের তত্ত্ব মতে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের কাজ করতে হাজার হাজার কোটি বছর প্রয়োজন। কিন্তু ডারউইনের বই প্রকাশের সময়ও সকল মানুষ বাইবেলীয় ব্যাখ্যা অনুযায়ী মনে করত, পৃথিবীর ব্যাস মোটে ছয় হাজার বছর। ১৮৬৬ সালে বিখ্যাত পদার্থ বিজ্ঞানী উইলিয়াম থমসন (পরবর্তী লর্ড কেলভিন উপাধিতে ভূষিত) বিবর্তন তত্বকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। থমসন রাসায়নিক শক্তি এবং মাধ্যাকর্ষণ এই দুইটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই আলাদা আলাদাভাবে সূর্যের ব্যাস নির্ধারণ করে দেখান, মাধ্যাকর্ষণ বল ব্যবহার করলে সূর্যের ব্যাস সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় এবং সেটাও কিনা হচ্ছে মাত্র কয়েক’শ লক্ষ বছর। এছাড়াও তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র ব্যবহার করে থমসন এটাও প্রমাণ করেন যে, মাত্র কয়েক লক্ষ বছর আগেও পৃথিবীর তাপমাত্রা এতই বেশি ছিল যে সেখানে কোনো রকম প্রাণের উৎপত্তি ঘটা ছিল একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। সুতরাং বিবর্তন হওয়ার কারণ হিসেবে ডারউইন যে প্রাকৃতিক নির্বাচন এবং এটির যে কোটি বছরের ক্রিকালের কথা বলছেন, তা অবাস্তব।
মজার ব্যাপার হলো, সেই সময় নিউক্লিয়ার শক্তি সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানীরা। বিংশ শতকের প্রথমদিকে শক্তির এই রূপ আবিষ্কার হওয়ার পর বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, ক্রমাগত নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদনের মাধ্যমে সূর্য এবং সকল তারা কোটি বছরেরও বেশি সময় একটি সুস্থিত শক্তির উৎস হিসেবে বিদ্যমান থাকে। সুতরাং কেলভিন বুঝতে পারলেন, সূর্য এবং পৃথিবীর বয়স নির্ধারণের জন্য তার করা হিসাবটি ভুল, এবং তিনি সেটা ১৯০৪ সালের ‘ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন মিটিং’-এ আংশিকভাবে স্বীকারও করে নেন। সুতরাং বিবর্তন তত্বকে নতুন একটি শক্তির উৎসের অনুমানদাতাও বলা যায়[৬৬]! উল্লেখ্য বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এসে পৃথিবীর নির্ভুল বয়স নির্ধারণ করা হয়, যা প্রায় সাড়ে চারশো কোটি বছর।
.
বিবর্তনের সত্যতা
সত্যতা প্রমাণ করা যায় সবদিক দিয়েই, তবে এইখানে আমরা মানুষের বিবর্তন নিয়েই আলোচনা করে দেখি বিবর্তন তত্ত্বের দাবি কতোটা সঠিক। বিবর্তনের প্রমাণ হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে ফসিল রেকর্ডকেই ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু আণবিক জীববিদ্যা এবং কোষবংশগতিবিদ্যা বিকশিত হবার পর এখন আর ফসিল রেকর্ডের কোনো দরকার নেই। জিনতত্ব দিয়েই চমৎকারভাবে বলে দেওয়া যায় আমাদের বংশগতিধারা। জীববিজ্ঞানের এই শাখার মাধ্যমে, আমাদের পূর্বপুরুষ কারা ছিল, তাদের বৈশিষ্ট্য কেমন ছিল অথবা দেখতে কেমন ছিল, সব নির্ণয় করা হয়েছে। দেখা গেছে ফসিল রেকর্ডের সাথে অক্ষরে অক্ষরে মিলেছে তা।
জীববিজ্ঞানীরা আমাদের পূর্বপুরুষের যে ধারাটা দিয়েছেন, সেটা হলো :
মানুষ→ নরবানর →পুরনো পৃথিবীর বানর → লিমার
প্রমাণ এক
রক্তকে জমাট বাঁধতে দিলে এক ধরনের তরল পদার্থ পৃথক হয়ে আসে, যার নাম সিরাম। এতে থাকে অ্যান্টিজেন। এই সিরাম যখন অন্য প্রাণীর শরীরে প্রবেশ করানো হয়, তখন উৎপন্ন হয় অ্যান্টিবডি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, মানুষের সিরাম যদি আমরা খরগোশের শরীরে প্রবেশ করাই তাহলে উৎপন্ন হবে অ্যান্টি হিউমান সিরাম। যাতে থাকবে অ্যান্টিডোন। এই অ্যান্টি হিউমান সিরাম অন্য মানুষের শরীরে প্রবেশ করালে অ্যান্টিজেন এবং অ্যান্টিবডি বিক্রিয়া করে অধঃক্ষেপ বা তলানি উৎপন্ন হবে। যদি একটি অ্যান্টি হিউম্যান সিরাম আমরা যথাক্রমে নরবানর, পুরনো পৃথিবীর বানর, লিমার প্রভৃতির সিরামের সাথে মেশাই তাহলেও অধঃক্ষেপ তৈরি হবে। মানুষের সাথে যে গ্রাণীগুলোর সম্পর্কের নৈকট্য সবচেয়ে বেশি বিদ্যমান সেই প্রাণীগুলোর ক্ষেত্রে তলানির পরিমাণ বেশি হবে, যত দূরের সম্পর্ক তত তলানির পরিমাণ কম হবে। তলানির পরিমাণ হিসাব করে আমরা দেখি, মানুষের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি তলানি পাওয়া যাচ্ছে, নরবানরের ক্ষেত্রে আরেকটু কম, পুরানো পৃথিবীর বানরের ক্ষেত্রে আরও কম। অর্থাৎ অনুক্রমটা হয়—
মানুষ → নরবানর → পুরনো পৃথিবীর বানর → লিমার
অঙ্গসংস্থানবিদদের মতে উল্লিখিত প্রাণীদের মধ্যে সর্বাধিক আদিম হচ্ছে লিমার, আর সবচেয়ে নতুন প্রজাতি হচ্ছে মানুষ। তাই মানুষের ক্ষেত্রে তলানির পরিমাণ পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি আর লিমারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে কম। দেখা যাচ্ছে বিবর্তন যে অনুক্রমে ঘটেছে বলে ধারণা করা হয়েছে রক্তরস বিজ্ঞানের অ্যান্টিজেন অ্যান্টিবডি বিক্রিও সে ধারাবাহিকতাকেই সমর্থন করে।
প্রমাণ দুই
১. প্রকৃতিতে মাঝে মাঝেই লেজ বিশিষ্ট মানব শিশু জন্ম নিতে দেখা যায়। এছাড়াও পেছনে পা বিশিষ্ট তিমি, ঘোড়ার পায়ে অতিরিক্ত আঙুল কিংবা পেছনের ফিন যুক্ত ডলফিনসহ শরীরে অসংগতি নিয়ে প্রাণীর জন্মের প্রচুর উদাহরণ পাওয়া যায়। এমনটা কেন হয়, এর উত্তর দিতে পারে কেবল বিবর্তন তত্বই। বিবর্তনের কোনো এক ধাপে অঙ্গ লুপ্ত হয়ে গেলেও জনপুঞ্জের জিনে ফেনোটাইপ বৈশিষ্ট্য হিসেবে ডিএনএ সেই তথ্য রেখে দেয়। যার ফলে বিরল কিছু ক্ষেত্রে তার পুনঃ প্রকাশ ঘটে।
২. বিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী পূর্ব বিকশিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকেই নতুন অঙ্গের কাঠামো তৈরি হয়। বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীর সামনের হাত বা অপদের মধ্যে তাই লক্ষণীয় মিল দেখা যায়। ব্যাঙ, কুমির, পাখি, বাদুড়, ঘোড়া, গরু, তিমি মাছ এবং মানুষের অগ্রপদের গঠন প্রায় একই রকম।
৩. পৃথিবীতে অগণিত প্রজাতি থাকলেও সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, ভেতরে আমরা সবাই প্রায় একই। আমরা সবাই ‘কমন জিন’ শেয়ার করে থাকি। পূর্বপুরুষের সাথে যত বেশি নৈকট্য বিদ্যমান, শেয়ারের পরিমাণও তত বেশি। যেমন, শিম্পাঞ্জি আর আধুনিক মানুষের ডিএনএ* শতকরা ৯৮% একই, কুকুর আর মানুষের ক্ষেত্রে সেটা ৭৫% আর ড্যাফোডিল ফুলের সাথে ৩৩%।
[* মানুষের দেহ অসংখ্য কোষ দিয়ে গঠিত। প্রতিটি কোষের একটি কেন্দ্র থাকে যার নাম নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াস-এর ভেতরে থাকে ক্রোমোজোম, জোড়ায় জোড়ায়। একেক প্রজাতির নিউক্লিয়াসে ক্রোমোজোম সংখ্যা একেক রকম। যেমন মানব কোষের নিউক্লিয়াসে ২৩ জোড়া ক্রোমোজোম থাকে। প্রতিটি ক্রোমোজোম-এর ভেতরে থাকে ডিএনএ এবং প্রোটিন। ডিএনএ এক ধরনের এসিড যা দেহের সকল কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করে। প্রকৃতপক্ষে ক্রোমোজোম-এর ভেতরে কী ধরনের প্রোটিন তৈরি হবে তা ডিএনএ নির্ধারণ করে। এসব প্রোটিনের মাধ্যমেই সকল শারীরবৃত্তীয় কাজ সংঘটিত হয়। ডিএনএ-র আরেকটি কাজ হচ্ছে রেপ্লিকেশন তথা সংখ্যাবৃদ্ধি। ডিএনএ নিজের হুবহু প্রতিলিপি তৈরি করতে পারে, ডিএনএই যেহেতু জীবনের মূল তাই আরেকটি প্রতিলিপি তৈরি হওয়ার অর্থই আরেকটি জীবন তৈরি হওয়া, এভাবেই জীবের বংশবৃদ্ধি ঘটে। মোটকথা ডিএনএ জীবনের মৌলিক একক এবং কার্যকরি শক্তি, সেই জীবের সকল কাজকর্ম পরিচালনা করে এবং তার থেকে আরেকটি জীবের উৎপত্তি ঘটায়। ডিএনএ-র মধ্যে তাই জীবের সকল বৈশিষ্ট্য ও বংশবৃদ্ধির তথ্য জমা করা থাকে। ডিএনএ-র মধ্যে থাকে জিন, জিনের সিকোয়েন্সই জীবদেহের সকল তথ্যের ভাণ্ডার।]
৪। চারপাশ দেখা হলো। এবার আসুন একবার নিজেদের দিকে তাকাই।
ক) ত্রয়োদশ হাড় : বাংলাদেশ মিলিটারি অ্যাকাডেমিতে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেলো আমার এক বন্ধু। বাক্স পেটরা বন্দি করে সে চলে গেল ট্রেনিংয়ে চট্টগ্রামের ভাটিয়ারীতে। ছয় সপ্তাহ ডলা খাবার পর মিলিটারি অ্যাকাডেমির নিয়ম অনুযায়ী একটি ফাইনাল মেডিক্যাল পরীক্ষা হয়। সেই পরীক্ষায় আমার বন্ধুর দেহ পরীক্ষা করে দেখা গেল, তার পাঁজরে এক সেট হাড় বেশি। আধুনিক মানুষের যেখানে বারো সেট হাড় থাকার কথা আমার বন্ধুর আছে তেরোটি। ফলস্বরূপ তাকে মিলিটারি অ্যাকাডেমির প্রশিক্ষণ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হলো। পরিসংখ্যান থেকে পাওয়া যায়, পৃথিবীর আটভাগ মানুষের শরীরে এই ত্রয়োদশ হাড়ের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যেটি কিনা গরিলা ও শিম্পাঞ্জির শারীরিক বৈশিষ্ট্য। মানুষ যে, এক সময় প্রাইমেট থেকে বিবর্তিত হয়েছে এই আলামতের মাধ্যমে সেটিই বোঝা যায়।
খ) লেজের হাড় : মানুষের আদি পূর্বপুরুষ প্রাইমেটরা গাছে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য লেজ ব্যবহার করত। গাছ থেকে নিচে নেমে আসার পর এই লেজের প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়েছে। কিন্তু আমাদের শরীরে মেরুদণ্ডের একদম নিচে সেই লেজের হাড়ের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।
ছবি। পেজ ৮৫
গ) আক্কেল দাঁত : পাথুরে অস্ত্রপাতি আর আগুনের ব্যবহার জানার আগে মানুষ মূলত নিরামিষাশী ছিল। তখন তাদের আক্কেল দাঁতের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও আমাদের তা নেই, যদিও আক্কেল দাঁতের অস্তিত্ব এখনও রয়ে গেছে।
ঘ) অ্যাপেন্ডিক্স : আমাদের পূর্বপুরুষ প্রাইমেটরা ছিল তৃণভোজী। তৃণজাতীয় খাবারে সেলুলোজ থাকে। এই সেলুলোজ হজম করার জন্য তাদের দেহে অ্যাপেন্ডিক্স বেশ বড় ছিল। ফলে সিকামে প্রচুর পরিমাণ ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারত যাদের মূল কাজ ছিল সেলুলোজ হজমে সহায়তা করা। সময়ের সাথে সাথে আমাদের পূর্বপুরুষদের তৃণজাতীয় খাবারের ওপর নির্ভরশীলতা কমতে থাকে, তারা মাংসাশী হতে শুরু করে। আর মাংসাশী প্রাণীদের অ্যাপেন্ডিক্সের কোনো প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন পড়ে বৃহৎ পাকস্থলীর। ফলে অপেক্ষাকৃত ছোট অ্যাপেন্ডিক্স এবং বড় পাকস্থলীর প্রাণীরা সংগ্রামে টিকে থাকার সামর্থ্য লাভ করে, হারিয়ে যেতে থাকে বাকিরা। পূর্বপুরুষের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে সেই অ্যাপেন্ডিক্স আমরা এখনও বহন করে চলছি।
ঙ) গায়ের লোম : মানুষকে অনেক সময় ‘নগ্ন বাঁদর’ বা ‘নেকেড এপ’ নামে সম্বোধন করা হয়। আমাদের অনেক বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেই লোমশ শরীরের অস্তিত্ব দেখা যায় এখনও। আমরা লোমশ প্রাইমেটদের থেকে বিবর্তিত হয়েছি বলেই এই আলামত এখনও রয়ে গেছে।
.
প্যালের চোখ
বিবর্তনতত্ত্বের সমালোচনাকারীরা সবচেয়ে বেশি আঙুল তুলেছেন মানুষের চোখের দিকে। চোখের মতো এমন নিখুঁত এবং জটিল একটি যন্ত্র কীভাবে দৈব পরিবর্তন (র্যান্ডম মিউটেশন), প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে সৃষ্টি হতে পারে? হোক না শত সহস্র বছর।
একটি ক্যামেরার মতো চোখেরও আলোকরশ্মি কেন্দ্রীভূত করার জন্য লেন্স, আলোকরশ্মির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আইরিস, আর এই আলোকরশ্মি থেকে ছবি আবিষ্কার করার জন্য একটি ফটো-রিসেপ্টর প্রয়োজন। এই তিনটি যন্ত্রাংশ একসাথে কাজ করলেই কেবল চোখ দিয়ে কিছু দেখা সম্ভব হবে। যেহেতু বিবর্তন তত্বমতে, বিবর্তন প্রক্রিয়া চলে স্তরে স্তরে-তাহলে লেন্স, রোটিনা, চোখের মণি সবকটি একসাথে একই ধরনের উৎকর্ষ সাধন করল কীভাবে? বিবর্তন সমালোচনাকারীদের প্রশ্ন এটাই।
ক্যামব্রিয়ান যুগে শরীরের ওপর আলোক সংবেদনশীল ছোট একটি স্থানবিশিষ্ট প্রাণীরা আলোর দিক পরিমাপের মাধ্যমে ঘাতক প্রাণীদের হাত থেকে বেঁচে যাওয়ার অতি সামান্য সুযোগ পেত। সময়ের সাথে সাথে এই রঙিন সমতল স্থানটি ভেতরের দিকে ডেবে গিযেছে, ফলে তাদের দেখার ক্ষমতা সামান্য বেড়েছে। গভীরতা বাড়ার পাশাপাশি পরবর্তীকালে আলো ঢোকার স্থান সরু হয়েছে। অর্থাৎ দেখার ক্ষমতা আরও পরিষ্কার হয়েছে। প্রতিটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিবর্তন প্রাণীকে সামান্য হলেও টিকে থাকার সুবিধা দিয়েছে।
সুইডেনের লুন্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড্যান এরিক নিলসন গবেষণার মাধ্যমে বের করে দেখান যে, কীভাবে একটি প্রাণীর শরীরের ওপর আলোক সংবেদনশীল ছোট এবং রঙিন স্থান পরবর্তীকালে মানুষের চোখের মতো জটিল যন্ত্রে পরিবর্তিত হতে পারে।
ছবি। পেজ ৮৮
চিত্র : পিংপং ডেমনস্ট্রেশন
উপরের ছবি দুটি লক্ষ্য করুন। বাম থেকে দ্বিতীয় ছবিতে একটি রুম, যেখানে একটি মাত্র বাতি বা আলোর উৎস আছে। প্রথম ছবিতে হাতে ধরা থাকা বোর্ডটি দিয়ে আমরা সে উৎসের দিকে তাকাই। সবচেয়ে বামের গর্তে সমতল কাগজ লাগানো। যার মাধ্যমে আমরা শুধু বুঝতে পারছি আলো আছে। কিন্তু কোথা থেকে আলো বের হচ্ছে কিংবা বাতিটি কোথায় তেমন কিছুই জানা যাচ্ছে না। তারপরের গর্তে একটি পিংপং বল রাখা। যে বলটির আলো প্রবেশের স্থানটি চওডা আর গভীরতা কম। এর মাধ্যমে আগের সাদা কাগজ থেকে কিছুটা ভালোভাবে আলোর উৎস সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব হচ্ছে। তার পরেরটার আলো প্রবেশের স্থান আগেরটার চেয়ে সংকুচিত এবং গভীরতা বেশি। সর্ব ডানেরটার আলো প্রবেশের স্থান সবচেয়ে সংকুচিত এবং গভীরতা সবচেয়ে বেশি। আর এটি দিয়েই আমরা সবচেয়ে ভালোভাবে আলোটির উৎস বুঝতে পারছি।
এখন প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব অনুযায়ী, প্রতিটি পরিবর্তনই প্রাণীকে কিঞ্চিৎ হলেও আক্রমণকারীর হাত থেকে বাঁচার সুবিধা প্রদান করেছে। যারা সামান্য দেখতে পাচ্ছে তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা বেড়েছে, বেড়েছে তাদের সন্তান বংশবৃদ্ধির সম্ভাবনা। অপরদিকে অথর্বরা হারিয়ে গেছে। ধীরে ধীরে বংশানুক্রমে উন্নতি হয়েছে দৃষ্টিশক্তির। সময়ের সাথে সাথে শুরুর এই আলোক সংবেদনশীল স্থান রেটিনায় পরিণত হয়েছে, সামনে একটি লেন্সের উৎপত্তি হয়েছে।
ছবি। পেজ ৮৯
চিত্র : পূর্ণাঙ্গ চোখের উদ্ভবের বিভিন্ন স্তর
ধারণা করা হয়, প্রাকৃতিকভাবে লেন্সের উৎপত্তি হয়েছে যখন চোখকে পূর্ণ করে রাখা স্বচ্ছ তরলের ঘনত্ব সময়ের সাথে সাথে বেড়েছে। ছবিতে দেখুন, সাদা অংশটি তৈরি হচ্ছে চোখকে পূর্ণ করে রাখা স্বচ্ছ তরলের মাধ্যমে। তরলের ঘনত্ব যত বেড়েছে লেন্সের গঠন তত ভালো হয়েছে, প্রখর হয়েছে দৃষ্টিশক্তি।
বলে রাখা প্রয়োজন বিজ্ঞানীদের তৈরি করা চোখের বিবর্তনের প্রতিটি স্তর বর্তমানে জীবিত প্রাণীদের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। এছাড়াও শুধু আলোক সংবেদনশীল স্থান বিশিষ্ট প্রাণী ছিল আজ থেকে ৫৫ কোটি বছর আগে। বিজ্ঞানীরা গণনা করে বের করেছেন, এই আলোক সংবেদনশীল চোখ ধীরে ধীরে মানুষের চোখের মতো হয়ে ওঠার জন্য সময় প্রয়োজন মাত্র ৩৬৪ হাজার বছর।
.
ডিজাইন না ব্যাড ডিজাইন?
মানুষের চোখের অক্ষিপটের ভেতরে এক ধরনের আলোগ্রাহী কোষ আছে যারা বাইরের আলো গ্রহণ করে এবং একগুচ্ছ অপটিক নার্ভের (আলোকগ্রাহী জাল) মাধ্যমে তাকে মস্তিষ্কে পৌঁছনোর ব্যবস্থা করে, ফলে আমরা দেখতে পাই। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, অক্ষিপটের ঠিক সামনে এই স্নায়ুগুলো জালের মতো ছড়ানো থাকে, এবং এই স্নায়ুগুলোকে যে রক্তনালীগুলো রক্ত সরবরাহ করে তারাও আমাদের অক্ষিপটের সামনেই বিস্তৃত থাকে। ফলে আলো বাধা পায় এবং আমাদের দৃষ্টিশক্তি কিছুটা হলেও ম্লান হয়ে যায়। স্নায়ুগুলোর এই অসুবিধাজনক অবস্থানের কারণে আমাদের চোখে আরেকটি বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে। স্নায়বিক জালটি মস্তিষ্কে পৌঁছনোর জন্য অক্ষিপটকে ফুটো করে তার ভিতর দিয়ে পথ করে নিয়েছে। এর ফলে উৎপত্তি হয়েছে একটি অন্ধবিন্দুর (blind spot)[৬৭]
কুকুর, বিড়াল কিংবা ঈগলের দৃষ্টিশক্তি যে মানুষের চোখের চেয়ে বেশি তা সবাই জানে। মানুষ তো বলতে গেলে রাতকানা, কিন্তু অনেক প্রাণীই আছে রাতে খুব ভালো দেখতে পায়। আবার অনেক প্রাণীই আছে যাদের চোখে কোনো অন্ধবিন্দু নেই। যেমন, স্কুইড বা অক্টোপাস। এদের মানুষের মতোই এক ধরনের লেন্স এবং অক্ষিপটওয়ালা চোখ থাকলেও অপটিক নার্ভগুলো অক্ষিপটের পেছনে অবস্থান করে এবং তার ফলে তাদের চোখে কোনো অন্ধবিন্দুর উৎপত্তি হয় নি।
মানুষের চোখের এই সীমাবদ্ধতাকে অনেকেই ‘ব্যাড ডিজাইন’ বলে অভিহিত করে থাকেন। অবশ্য চোখ দিয়ে যেহেতু ভালোভাবেই কাজ চালিয়ে নেওয়া যাচ্ছে তাই ‘ব্যাড ডিজাইন’-এর মতো শব্দ প্রযোগে নারাজ জীববিজ্ঞানী কেনেথ মিলার। তার মতে, চোখের এমন হওয়ার কারণ বিবর্তন তত্ব দিয়ে বেশ ভালোভাবে বোঝা যায়[৬৮]। বিবর্তন কাজ করে শুধু ইতোমধ্যে তৈরি বা বিদ্যমান গঠনকে পরিবর্তন করার মাধ্যমে, সে রাতারাতি নতুন করে কিছু সৃষ্টি করে ফেলতে পারে না। মানুষের মতো মেরুদণ্ডী প্রাণীর চোখ তৈরি হয়েছে অনেক আগেই। উদ্ভূত হওয়া মস্তিষ্কের বাইরের দিকের অংশকে পরিবর্তন করে। বহুকাল ধরে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্কের বাইরের দিক আলোক সংবেদনশীল হয়েছে, তারপর ধীরে ধীরে অক্ষিপটের আকার ধারণ করেছে। যেহেতু মস্তিষ্কের পুরনো মূল গঠনটি বদলে যায় নি, তাই জালের মতো ছড়িযে থাকা স্নায়ুগুলোও তাদের আগের অবস্থানেই রয়ে গেছে। কিন্তু অন্যদিকে স্কুইড জাতীয় প্রাণীর চোখ বিবর্তিত হয়েছে তাদের চামড়ার অংশ থেকে, মস্তিষ্কের অংশ থেকে নয়। এক্ষেত্রে ত্বকের স্নায়ুগুলো মস্তিষ্কের মতো ঠিক বাইরের স্তরে না থেকে ভেতরের স্তরে সাজানো থাকে, আর এ কারণেই স্নায়ুগুলো চোখের অক্ষিপটের সামনে নয় বরং পেছনেই রয়ে গেছে। চোখের ক্ষেত্রে তাই গুড ডিজাইন বা ব্যাড ডিজাইন তর্ক অপ্রাসঙ্গিক। এটাকে তো আদপে ডিজাইনই করা হয় নি।
ছবি। পেজ ৯২
চিত্র : মানুষের চোখের ভেতরে তৈরি হওয়া অন্ধবিন্দু
বিবর্তনের পথে অন্তত চল্লিশ রকমভাবে চোখ তৈরি হতে পারত[৬৯]। আলোকরশ্মি শনাক্ত এবং কেন্দ্রীভূত করার আটটি ভিন্ন উপায়ের সন্ধান দিয়েছেন নিউরো বিজ্ঞানীরা[৭০]। কিন্তু পরিবেশ এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের যুদ্ধে অসংখ্য সমাধানের মধ্যে একটি সমাধান টিকে গিয়েছে। সংক্ষেপে, চোখের গঠন যদি বাইরের কারও হস্তক্ষেপ ব্যতীত, শুধু বস্তুগত প্রক্রিয়ায় উদ্ভব হতো তাহলে দেখতে যেমন হওয়ার কথা ছিল ঠিক তেমনই হয়েছে। চোখের গঠনে কারও হাত নেই, নেই কোনো মহাপরাক্রমশালী নকশাকারকের নিপুণতা।
.
অসম্ভাব্যতা
বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় ইসলামি পণ্ডিত জাকির নায়েকের বিবর্তন তত্ব নিয়ে সাত মিনিটের লেকচারটি অনলাইন মিডিয়ায় খুবই জনপ্রিয়। সাত মিনিটে প্রায় ২৮টি মিথ্যা বা ভুল কথার মাধ্যমে জাকির নায়েক ডারউইনের বিবর্তন তত্ব ভুল প্রমাণ করতে না পারলেও সৃষ্টিবাদীরা কতটা অজ্ঞ তা ঠিকই প্রমাণ করেছেন[৭১]। এই সাত মিনিটের মধ্যে মাত্র পাঁচ সেকেন্ড সময় জাকির নাযেক বিবর্তন ঘটার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেছেন হাসতে হাসতে, কারণ তার মতে, এটা সবাই বুঝতে পারে এপ (Ape) থেকে বিবর্তিত হয়ে মানুষ হওয়ার সম্ভাবনা কী পরিমাণ ক্ষুদ্র প্রায় সকল সৃষ্টিবাদীরা এক প্রজাতি থেকে অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনাকে শূন্যের কাছাকাছি রায় দিয়ে বিবর্তন তত্ত্বকে বাতিল করে দেন।
অনেকে অনেকভাবে বললেও সবচেয়ে যথাযথ যুক্তিটা এমন, এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীতে পরিবর্তনের জন্য আলাদা-আলাদা অসংখ্য মিউটেশন হতে হবে। প্রতিটি মিউটেশন হওয়ার সম্ভাবনাই যেখানে প্রায় শূন্যের কাছাকাছি, সেখানে সবগুলো একসাথে হয়ে আলাদা একটি প্রাণী সৃষ্টি হওযা অকল্পনীয় ব্যাপার। ধরা যাক, একটি ছক্কার গুটি পাঁচবার নিক্ষেপ করা হবে। পাঁচবার নিক্ষেপে যদি পর্যায়ক্রমে ৩, ২, ৬, ২, ৫ উঠে আসে তাহলে ধরে নেওয়া হবে যে একটি প্রাণী থেকে আরেকটি প্রাণী বিবর্তিত হলো। এখন পাঁচবার ছক্কা নিক্ষেপ করে ৩, ২, ৬, ২, ৫ পাওয়ার সম্ভাবনা ১/৬ × ১/৬ × ১/৬ × ১/৬ × ১/৬ বা ১/৭৭৭৬ = ৭৭৭৬ বারে একবার। একটি নতুন প্রজাতির বিবর্তন কিংবা একটি নতুন অঙ্গের বিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা এরচেয়ে অনেক অনেক কম, সুতরাং বিবর্তন একটি অসম্ভব ব্যাপার!
উপরের উদাহরণে সম্ভাবনার যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে তাতে আপত্তি না থাকলেও বিবর্তনের সাথে একে মেলানো মারাত্মক ত্রুটিপূর্ণ এবং অপ্রাসঙ্গিক। চোখের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি, বিবর্তন হওয়ার জন্য অসংখ্য পথ খোলা থাকে। এখন একটি পথ গ্রহণ করে ফেলার পর আমরা যদি সেই পথটি গ্রহণ করার সম্ভাবনা হিসাব করি তাহলে সেটা যুক্তিসংগত হবে না। উদাহরণের মাধ্যমে কথাটা পরিষ্কার করা যাক।
একটি তাসের প্যাকেটে বাহান্নটি তাস থাকে। এখন দোকান থেকে প্যাকেট কিনে, আমরা টেবিলের ওপর সেগুলো সাজালাম। ধরি, আমাদের সামনে ১০৬৮ (১ এরপর ৬৮টি শূন্য) টি তাস আছে। এখন তাসগুলোকে বস্তায় ভরে ঝাঁকাতে শুরু করি। ঝাঁকানো শেষে আমরা বস্তা থেকে ছয়টি কার্ড বের করব। ধরা যাক, আমরা প্রথমে পেলাম স্পেড-এর টেক্কা। এরপর যথাক্রমে ডাইসের সাত, ক্লাবসের দশ, ক্লাবসের বিবি, ডাইসের দুই, হার্টসের রাজা। এখন হাতের মধ্যে প্রাপ্ত অনুক্রমের পাঁচটি তাস ধরে আমরা যদি ১০৬৮ টি তাসের মধ্য থেকে এদের পাওয়ার সম্ভাবনা বের করে বলি যে, প্রাপ্ত অনুক্রমটি পাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষুদ্র, সুতরাং এই পাঁচটি তাস পাওয়া অসম্ভব, তাহলে কী হবে? হবে না। বস্তায় ঝাঁকি দিয়ে পাঁচটা হোক, দশটা হোক, যে কয়টি তাসই আমরা বের করি না কেন, সবসময়ই একটি অনুক্রম পাব এবং সবসময়ই সেই নির্দিষ্ট অনুক্রম পাওয়ার সম্ভাবনা শূন্যের কাছাকাছি হবে। তার মানে এই না যে আমাদের সম্ভাবনা হিসাব শেষ করার পর। হাত থেকে তাসগুলো উধাও হয়ে যাবে।
বিবর্তন তত্ত্ব অনুসারে, ইতস্ততবিক্ষিপ্ত মিউটেশনের কারণে জনপুঞ্জে অসংখ্য ভ্যারিয়েশন তৈরি হয়। ব্যাপারটাকে তুলনা করা যায় স্পেইড ট্রাম্প থেলার সাথে চার জন খেলোয়াড়, বণ্টনে সবাই ১৩টি করে তাস পাবেন। এখন এই চারজনের মধ্যে এক জনের হাতে বাকি তিন জন অপেক্ষা ভালো তাস থাকবে, সুতরাং তিনি জিতবেন। প্রকৃতিতেও নন র্যান্ডম প্রাকৃতিক নির্বাচনের কারণে সবচেয়ে উপযোগীরা টিকে থাকে, বাকিরা ঝরে পড়ে। স্পেইড ট্রাম্পে জয়ী মানুষটির হাতের কার্ড দেখে কেউ যদি মন্তব্য করে এমন কম্বিনেশন পাওয়া অসম্ভব, তাহলে তাকে কী বলা যাবে? একইভাবে প্রকৃতিতে ইতোমধ্যে টিকে থাকা এক জনকে ধরে কেউ যদি সম্ভাবনা হিসাব করে এবং বলে যে সম্ভাবনা খুব কম, সুতরাং এটি ঘটে নি তাহলে সেটা নিঃসন্দেহে ভ্রান্তিপূর্ণ। শুধু বিবর্তন নয়, প্রাণের উৎপত্তির ক্ষেত্রেও যে এধরনের গণনা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে, এটা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই বইয়ের ‘ফ্রেডরিক হয়েলের। বোয়িং ৭৪৭ ফ্যালাসি’ অধ্যায়ে।
.
বিহে’র হ্রাস অযোগ্য জটিলতা
প্যালের মতো আরেকজন বিখ্যাত সৃষ্টিবাদের প্রবক্তা মাইকেল বিহে। ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত তার জনপ্রিয় বই, ‘Darwin’s Black Box : The Biochemical Challenge to Evolution’ এ তিনি ‘Irreducible Complexity’ বা হ্রাস অযোগ্য জটিলতা নামে নতুন এক শব্দমালা পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, একটি নির্দিষ্ট যন্ত্রে বেশ কয়েকটি অংশ থাকে এবং এদের মধ্য থেকে যেকোনো একটি অকেজো হলে, বা না থাকলে সেটি আর কাজ করে না। তিনি তার বইয়ে বলেন–
যে সমস্ত জৈব তন্ত্র (Biological System) নানা ধরনের, পর্যায়ক্রমিক কিংবা সামান্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কোনোভাবেই গঠিত হতে পারে না, তাদের আমি ‘হ্রাস অযোগ্য জটিল’ (Irreducible Complex) নামে অভিহিত করি। ‘হ্রাস অযোগ্য জটিলতা’ আমার দেওয়া এক বর্ণাঢ্য শব্দমালা যার মাধ্যমে আমি পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ায় অংশ নেওয়া একাধিক যন্ত্রাংশের একটি সিস্টেম বোঝাই-যার মধ্য থেকে একটি অংশ খুলে নিলেই সিস্টেমটি কাজ করবে না। ইঁদুর মারার যন্ত্রকে তিনি উদাহরণ হিসেবে টেনে আনেন। এ যন্ত্রটির মধ্যে কয়েকটি অংশ থাকে : ১. কাঠের পাটাতন ২. ধাতব হাতুড়ি, যা ইঁদুর মারে, ৩. ম্পিং, যার শেষ মাথা হাতুডির সাথে আটকানো থাকে ৪. ফাঁদ যা স্প্রিংটিকে বিমুক্ত করে ৫. ধাতব দণ্ড যা ফাঁদের সাথে যুক্ত থাকে এবং হাতুডিটিকে ধরে রাখে[৭২]? এখন যদি যন্ত্রটির একটি অংশ (সেটি স্প্রিং হতে পারে, হতে পারে ধাতব কাঠামো) না থাকে বা অকেজো থাকে, তাহলে সম্পূর্ণ যন্ত্রটিই অপ্রয়োজনীয় হয়ে যায়। এটি আর ইঁদুরকে মারা তো দূরের কথা, ধরতেও পারবে না। বিহে’র মতে, এটি হ্রাস অযোগ্য জটিল সিস্টেমের একটি ভালো উদাহরণ। এখানে প্রতিটি অংশের আলাদা কোনো মূল্য নেই। যখন তাদের একটি বুদ্ধিমান মানুষ দ্বারা প্রয়োজন মোতাবেক একত্রিত করা হয়, তখনই এটি কর্মক্ষম হয়ে ওঠে। ঠিক একইভাবে বিহে মনে করেন, প্রকৃতিতে ব্যাকটেরিয়ার ক্ল্যাজেলামগুলো হ্রাস অযোগ্য জটিল। এ ফ্ল্যাজেলামগুলোর প্রান্তদেশে এক ধরনের জৈবমটর আছে যেগুলোকে ব্যাকটেরিয়ার কোষগুলো স্ব প্ৰচালনের কাজে ব্যবহার করে। তার সাথে চাবুকের মতো দেখতে এক ধরনের প্রপেলারও আছে, যেগুলো ঐ আণবিক মটরের সাথে ঘুরতে পারে। প্রোপেলারগুলো একটি ইউনিভার্সাল জয়েন্টের মাধ্যমে মোটরের সাথে লাগানো থাকে। মোটরটি আবার এক ধরনের প্রোটিনের মাধ্যমে আগামতো রাখা থাকে, যেগুলো বিহে’র মতে স্ট্যাটারের ভূমিকা পালন করে। আরেক ধরনের প্রোটিন বুশিং পদার্থের ভূমিকা পালন করে, যার ফলে চালক স্তম্ভদণ্ডটি ব্যাকটেরিয়ার মেমব্রেনকে বিদ্ধ করতে পারে। বিহে বলেন, ব্যাকটেরিয়ার ক্ল্যাজেলামকে ঠিকমতো কর্মক্ষম রাখতে ডজন খানেক ভিন্ন ভিন্ন প্রোটিন সম্মিলিতভাবে কাজ করে। যেকোনো একটি প্রোটিনের অভাবে ফ্ল্যাজেলাম কাজ করবে না, এমনকি কোষগুলো ভেঙে পড়বে[৭৩]।
বিহে জানতেন না যে, ‘হ্রাস অযোগ্য জটিলতা’ নামক শব্দের ব্যঞ্জনায় বিবর্তনকে ভুল প্রমাণে বই লেখার প্রায় ষাট বছর আগেই নোবেল বিজয়ী হারমান জোসেফ মুলার বিবর্তনের হ্রাস অযোগ্য জটিলতা ব্যাখ্যা করেছিলেন, তখন থেকেই সেটা বিহে ব্যতীত অন্য সকলের কাছে ছিল জীববিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান হিসেবে জ্ঞাত। বিশেষত জিনের বিমোচন এবং প্রতিলিপিকরণ খুবই সাধারণ, যার মাধ্যমে হ্রাস অযোগ্য জটিলতার মতো বৈশিষ্ট্য সহজেই তৈরি হতে পারে[৭৫, ৭৬]। বিবর্তনের পথ ধরে বইয়ের, ‘ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন : সৃষ্টিতত্ত্বের বিবর্তন’ প্রবন্ধে বন্যা আহমেদ অধ্যাপক বিহে’র যুক্তির অযৌক্তিকতা খণ্ডন করতে গিয়ে বলেছেন–
বিহে’র উদাহরণে বর্ণিত ঐ ইঁদুর মারার কলটির কথাই ধরুন। কলটি স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে খুলে এর ফাঁদ এবং ধাতব দণ্ডটি সরিয়ে নিন। এবার আপনার হাতে যেটি থাকবে সেটি আর ইঁদুরের কল নয়, বরং অবশিষ্ট তিনটি যন্ত্রাংশ দিয়ে গঠিত মেশিনটিকে আপনি সহজেই টাই ক্লিপ কিংবা পেপার ক্লিপ হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন। এবারে স্প্রিংটিকে সরিয়ে নিন। এবারে আপনার হাতে থাকবে দুই-যন্ত্রাংশের চাবির চেইন। আবার প্রথমে সরিয়ে নেওয়া ফাঁদটিকে মাছ ধরার ছিপ হিসেবেও আপনি ব্যবহার করতে পারবেন, ঠিক যেমনিভাবে কাঠের পাটাতনটিকে ব্যবহার করতে পারবেন, ‘পেপার ওযেট’ হিসেবে। অর্থাৎ যে সিস্টেমটিকে এতক্ষণ হ্রাস অযোগ্য জটিল বলে ভাবা হচ্ছিল, তাকে আরও ছোট ছোটভাবে ভেঙে ফেললে অন্যান্য অনেক প্রয়োজনীয় কাজে লাগানো যায়।
ছবি। পেজ ৯৯
চিত্র : ইঁদুর মারার যন্ত্র এবং বিহে’র হ্রাস অযোগ্য জটিলতা
মজার ব্যাপার হলো, বিবর্তনের পথে প্রাণীদের ধর্ম বা গুণাবলির পরিবর্তন হয়। চাবির চেইন থেকে পেপার ক্লিপ, পেপার ক্লিপ থেকে আবার ইঁদুর কল, গুণাবলির এমন পরিবর্তন (আক্ষরিক ভাবে পেপার ক্লিপ বা চাবির রিং বোঝানো হচ্ছে না) যে প্রাণিজগতেও হচ্ছে সেটা বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন[৭৭]। কীভাবে এমনটি ঘটে সেটির ব্যাখ্যা বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানে একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য। নির্দিষ্ট একটি জৈবযন্ত্র শুরুতে এক ধরনের কাজ করলেও প্রাকৃতিক নির্বাচনের কারণে ক্রমান্বয়ে দেহের জটিলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সেই নির্দিষ্ট যন্ত্র ভিন্ন ধরনের কাজ করার ক্ষমতা লাভ করে। মানুষের চোখের বিবর্তনের অংশে ঠিক এমন জিনিস আমরা দেখেছি। যেমন, পাখির পালক যখন প্রথমে উদ্ভূত হয়েছিল, সেটা আকাশে উড়ার কথা মাথায় রেখে হয়নি, বরং তার দেহের তাপমাত্রাকে নিয়ন্ত্রণ করাই ছিল মুখ্য, পরবর্তীতে বিবর্তনের অসংখ্য ধাপ পেরিয়ে অনেক পরে। সেটা ডানায় রূপান্তরিত হয়ে পাখিকে উড়ার ক্ষমতা এনে দিয়েছে।
এবার আসা যাক ফ্ল্যাজেলাম আর প্রোটিনের আলোচনায়। ‘বিবর্তন পথ ধরে’ বই থেকে পুনরায় উদ্ধৃত–
বিহে যেমন ভেবেছিলেন কোনো প্রোটিন সরিয়ে ফেললে ফ্ল্যাঙ্গেলাম আর কাজ করবে না, অর্থাৎ পুরো সিস্টেমটিই অকেজো হয়ে পড়বে, তা মোটেও সত্য নয়। ব্রাউন ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক কেনেথ মিলার পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রোটিন সরিয়ে ফেলার পরও ফ্ল্যাজোলামগুলো কাজ করছে; বহু ব্যাকটেরিয়া এটিকে অন্য কোষের ভেতরে বিষ ঢেলে দেওয়ার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করতে পেরেছেন যে, ফ্ল্যাজেলামের বিভিন্ন অংশগুলো আলাদা আলাদাভাবে ভিন্ন কাজ করলেও প্রাকৃতিক নির্বাচনের কারণে এটি টিকে থাকার সুবিধা পেতে পারে। জীববিজ্ঞানে এমন অনেক উদাহরণ দেওয়া যায় যে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো একসময় এক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হলেও পরবর্তীকালে অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে। সরীসৃপের চোয়ালের হাড় থেকে স্তন্যপায়ী প্রাণীর কানের উৎপত্তি। আজকে আমাদের কানের দিকে তাকালে সেটিকে ‘হ্রাস অযোগ্য জটিল’ মনে হতে পারে, কিন্তু আদিকালে। তা ছিল না। এমন নয় যে, হঠাৎ করেই একদিন স্তন্যপায়ী প্রাণীদের কজা বিহীন চোয়ালের হাডগুলো ঠিক করল তারা কানের হাড়ে পরিণত হয়ে যাবে; বরং বিবর্তনের পথ ধরে অনেক চড়াই উৎরাই পেরিযেই তারা আজকের রূপ ধারণ করেছে। সুতরাং উৎপত্তির সামগ্রিক ইতিহাস না জেনে শুধু চোখ, কান কিংবা ফ্ল্যাজেলামের দিকে তাকালে এগুলোকে ‘হ্রাস অযোগ্য জটিল’ বলে মনে হতে পারে বৈকি।
জীববিজ্ঞানের গবেষণাপত্রে স্তন্যপায়ীদের কানের মতো অসংখ্য উদাহরণ চোখে পড়বে। জীবাশ্মবিজ্ঞানী স্টিফেন জে. গুল্ড পাণ্ডার বৃদ্ধাঙ্গুলির মাধ্যমে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করছেন সবচেয়ে সফলভাবে[৭৮]। পাণ্ডার হাতে ছয়টি করে আঙুল থাকে। এর মধ্যে বৃদ্ধাঙ্গুলিটি আদতে আঙুল নয়, বরঞ্চ কবজির হাড় যেটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পাণ্ডার একমাত্র খাবার বাঁশ ধরে রাখার সুবিধার্থে আঙুলে পরিণত হয়েছে। যাই হোক, বিহে তার বইয়ে এমন আরও উদাহরণ হাজির করেছেন যার প্রায় সবগুলোই বিজ্ঞানীরা বিবর্তনের আলোকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। বিহে’র ইচ্ছা ছিল, শূন্যস্থান খুঁজে সেখানে কোনো ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনার বসিয়ে দেওয়া, কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, শূন্যস্থানটাও তিনি ঠিকমতো খুঁজে বের করতে পারেন নি।
উইলিয়াম প্যালে যখন প্রথম আঠারো শতকে ‘আর্গুমেন্ট অব ডিজাইন’ বা সৃষ্টির অনুকল্পের অবতারণা করেছিলেন, তখন তিনি চোখের গঠন দেখে যারপরনাই বিস্মিত হয়েছিলেন। প্যালে ভেবেছিলেন চোখের মতো একটি জটিল প্রত্যঙ্গ কোনোভাবেই প্রাকৃতিক উপায়ে বিবর্তিত হতে পারে না। কিন্তু আজকের দিনের জীববিজ্ঞানীরা পর্যাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রাকৃতিক নিয়মে চোখের বিবর্তনের ধাপগুলো সম্বন্ধে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়েছেন। ম্যাট ইং তার একটি প্রবন্ধে বলেন- ‘আধা চোখের যুক্তি’ গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না দেখে ড. বিহে এখন আধা ফ্ল্যাজেলামের যুক্তি হাজির করেছেন; আর একটা গালভরা নামও খুঁজে বের করেছেন– ‘ইরিডিউসিবল কমপ্লেক্সিটি’। কিন্তু এটি ওই পুরনো আধা চোখের যুক্তিই। বানানো এই গালভরা পরিভাষাটি বাদ দিলে এটি শেষ পর্যন্ত ওই অজ্ঞতাসূচক যুক্তি বা ‘গড ইন গ্যাপস্’[৭৯] ছাড়া আর কিছু নয়।
.
ডেম্বস্কির গাণিতিক চালাকি
সেদিন চার মাসের তাবলীগ থেকে ফেরত আসা এক বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ যে আছে এটা তুই কীভাবে জানিস? সে নির্দোষ জবাব দিল, চারপাশের এইসব সৃষ্টি দেখলে তো বোঝা যায় যে আল্লাহ আছেন। আমি ততোধিক নির্দোষ ভঙ্গিতে জবাব দিলাম, এমন কী হতে পারে না, আল্লাহ এদের সৃষ্টি করেন নি? তখন সে জানালো, তাহলে কি এমনি এমনি হয়েছে? এই নিবন্ধের শিরোনামও একটি বহুল প্রচারিত ইসলামিক গান যেখানে স্রষ্টার সুনিপুণ কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া, সাধারণভাবে আমরা সবাই জগতের নানা ধরনের জটিল ব্যাপার দেখে এতটাই বিমোহিত হই যে, এগুলো যে নিজে নিজে এমন হতে পারে কিংবা প্রাকৃতিক কারণে এমন হতে পারে তা মেনে নেওয়াটাকে পাগলামি বলে ঠাওর হয়। আর সেটাকেই ব্যবহার করে যুক্তি (!) উপস্থাপন করেন প্যালে, বিহে’র মতো ধর্মবেত্তারা।
ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের খ্যাতনামা আরেকজন প্রবক্তা উইলিয়াম ডেম্বস্কি। এই সময় পর্যন্ত ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন সমর্থন করে বিহে’র বই সংখ্যা একটি হলেও তার ডিসকভারি ইন্সটিটিউটের (আইডি প্রচারণার কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে পরিচিত) আরেকজন সহকর্মী ডেম্বস্কির বইয়ের সংখ্যা বেশ কয়েকটি এবং নিবন্ধের সংখ্যা অসংখ্য[৮০]। প্যালে, বিহে’র থেকে দশ গুণ এগিয়ে থাকা ডেম্বস্কি প্রচার করে বেড়ান প্রকৃতির ডিজাইনড়’ হওয়ার বিষয়টি গাণিতিকভাবে প্রমাণযোগ্য। তার মতে, প্রকৃতির বিভিন্ন জায়গায় ‘সুনির্দিষ্টভাবে উপস্থাপিত তথ্য’-এর সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৯৯ সালে প্রকাশিত বই ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন’-এ ডেম্বস্কি একটি উদাহরণ প্রদান করার পর বলেন, যেহেতু কোনো বস্তুতে সাধারণ প্রাকৃতিক উপায়ে সুনির্দিষ্ট তথ্য উৎপাদন হওয়া অসম্ভব, সুতরাং এটা সহজেই বোধগম্য, কোনো একজন পরিকল্পক বা ডিজাইনার এই কাজটি করেছেন তার অস্তিত্বের প্রমাণ মানুষকে অবহিত করতে[৮১]। বক্তব্যকে যুক্তিসংগত করতে তিনি কার্ল সাগানের উপন্যাস ‘কনট্যাক্ট’ অবলম্বনে তৈরি একই নামের চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গ টেনে আনেন[৮২]। এই চলচ্চিত্রে পৃথিবীর জ্যোতির্বিদরা একটি এক্সট্রা টেরেস্ট্রিয়াল বার্তার সন্ধান লাভ করেন, যেটি ভাষান্তর করে তারা দেখতে পান মহাশূন্যের অপর প্রান্ত থেকে ‘কে বা কারা তাদের কাছে ২ থেকে ১০১ পর্যন্ত প্রত্যেকটি প্রাইম সংখ্যা পাঠিয়েছেন। আর এই প্রাইম সংখ্যা পাওয়ার পর চলচ্চিত্রের জ্যোতির্বিদরা বুঝতে পারেন, বার্তাটি যেই পাঠিয়ে থাকুক না কেন, সে অবশ্যই বুদ্ধিমান। ডেম্বস্কি তারপর উপসংহার টানেন যে, প্রকৃতিতে প্রাপ্ত এমন সুনির্দিষ্ট গাণিতিক তথ্যও নিশ্চিত করে যে, এই তথ্যগুলো জগতের বাইরের কারো কাজ এবং তিনিই মহাপরিকল্পক, ডিজাইনার ঈশ্বর।
কিন্তু একটি সুশৃঙ্খল গাণিতিক ক্ৰমের সন্ধান পাওয়ার জন্য ডেম্বস্কির বহির্বিশ্বের কারও সংকেতের জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। তার বাসার পাশে ফুলের বাগান আছে কিনা আমাদের জানা নেই, যদি থাকে তাহলে সে বাগানে গিয়ে বিভিন্ন ফুলের পাপডির সংখ্যা গণনা করলেই তিনি প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত চমৎকার গাণিতিক ক্ৰমের সন্ধান পাবেন, যাকে গণিতে বলা হয় ফিবোনাচি রাশিমালা। ফিবোনাচি রাশিমালা অনেকগুলো সংখ্যার একটি সেট যেখানে প্রতিটি সংখ্যা তার পূর্ববর্তী দুইটি সংখ্যার যোগফলের সমান : ০, ১, ১, ২, ৩, ৫, ৮, ১৩, ২১, ৩৪, ৫৫, …] প্রকৃতির অসংখ্য ফুলের সর্বমোট পাপডি সংখ্যা একটি ফিবোনাচি রাশি। যেমন : বাটারকাপের পাপড়ি সংখ্যা ৫, গাঁদা ফুলের ১৩, এসটার্সের ২১
তবে একটা বিষয় বোঝা যাচ্ছে প্যালে, বিহে’র তুলনায় ডেম্বস্কির দাবি অনেক বেশি ব্যবহারিক ও প্রযুক্তি নির্ভর। সুতরাং এগুলো ঠিকমতো উপলব্ধি করা এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য প্রয়োজন বিশেষজ্ঞ মানুষ। ঘটনাক্রমে অনেক বিশেষজ্ঞই এই কষ্টটুকু গ্রহণ করেছেন এবং তাদের প্রত্যেকেই দেখিয়েছেন ডেম্বস্কির উপস্থাপিত প্রতিটি দাবি এবং তা থেকে টেনে আনা উপসংহারটি মারাত্মক ত্রুটিযুক্ত[৮৩]।
.
আর্গুমেন্ট ফ্রম ব্যাড ডিজাইন
সৃষ্টির সুনিপুণ নকশা বা ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন নিয়ে মানুষের কী মাতামাতি! এই মাজেজা তারা স্কুল, কলেজের পাঠ্যপুস্তকেও অন্তর্ভুক্ত করতে চায়। আরে ভাই, নিজের শরীরের দিকেই একটু তাকিয়ে দেখুন না। এটা কি ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের কোনো নমুনা? একজন ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনার কি তার ডিজাইনে কখনও বিনোদন স্থানের পাশে প্যঃনিষ্কাশন পাম্প রাখবেন?[৮৪]
কথাটি বলেছিলেন কৌতুকাভিনেতা রবিন উইলিয়ামস তার অভিনীত চলচ্চিত্র ম্যান অব দ্য ইয়ার’ এ চলচ্চিত্রে রবিন একজন নগণ্য টেলিভিশন টক-শো অনুষ্ঠানের উপস্থাপক থেকে নানা ঘটনা, দুর্ঘটনার মাধ্যমে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হয়ে যান। প্রথা অনুযায়ী প্রাক নির্বাচন বিতর্কে তাকে যখন ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় তখন এই ছিল তার উত্তর। কৌতুক করে বললেও কথাটা গুরুত্বপূর্ণ। যদিও মানুষের শরীরের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আপাতদৃষ্টিতে ভালোভাবেই কাজ করছে এবং আমাদেরও বিনোদনের জায়গায় কাছাকাছি অন্য কিছুর সহাবস্থানের ব্যাপারে তেমন কোনো অভিযোগ নেই, তবুও আমাদের আজন্ম লালন করা ‘সুনিপুণ নকশা প্রবাদটি মানসিক ভ্রম ছাড়া আর কিছুই নয়। ঠিক মতো বিচার করলে প্রতিটি প্রজাতির নকশায় কিছু না কিছু ত্রুটি আছে। কিউই (Kiwi)-র অব্যবহৃত ডানা, তিমির ভেস্টিজ্যিাল পেলভিস, আমাদের অ্যাপেন্ডিক্স যা শুধু অকাজেরই না বরঞ্চ কখনো কখনো এটি মৃত্যুর কারণও হয়ে দাঁড়ায়[৮৫]।
এই লেখার শুরুতে আমরা দেখেছি ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের প্রবক্তা প্যালে, বিহেরা মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের সাথে তুলনা করেছিলেন ডিজাইন করা একটি ঘড়ি বা ইঁদুর মারা কলের সাথে বিহে’র ইঁদুর মারার কলে প্রতিটি যন্ত্রাংশ-কাঠের পাটাতন, ধাতব হাতুডি, স্প্রিং, ফাঁদ, ধাতব দণ্ড খুব সতর্কভাবে এমনভাবে জোড়া দেওয়া হয়েছে যেন অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এটি ইঁদুর মারার কাজটি করতে পারে। এখন প্রতিটা যন্ত্রাংশ আরও ভালোভাবে তৈরি করতে গেলে ইঁদুর মারার যন্ত্র বলুন আর ঘড়ির কথা বলুন মূল ডিজাইনে নতুন করে কিছু করার থাকে না। এবং আরও মনে রাখা দরকার ঘড়ি, ইঁদুর মারার কলসহ মানুষের তৈরি প্রতিটি যন্ত্রে কখনও অপ্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশের উপস্থিতি দেখা যায় না। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাক। ঘটনাটি এ বইয়ের সহলেখক রায়হান আবীরের। তিনি তখন সবেমাত্র পিএইচডি করার জন্য ভর্তি হয়েছেন। তিনি বায়োমেডিক্যাল ফিজিক্স এন্ড টেকনোলজি বিভাগের যে ল্যাবে কাজ করতেন সেখানে চা বানানোর জন্য পানি গরম করার একটি হিটার ছিল। কিন্তু এই হিটারে পানি দিয়ে সবাই সবসময়ই সেটা বন্ধ করার করার কথা। ভুলে যেতেন। পরে ঠিক করা হলো, একটা টাইমার সার্কিট তৈরি করে হিটারের সাথে সংযুক্ত করে দেওয়া হবে : সেটিতে তিনটি সুবিধা থাকবে। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট, পনেরো মিনিট এই তিন সময়ে এটি বন্ধ করা যাবে। ফলে পানি গরম করতে দিয়ে কারো আর চিন্তা করতে হবে না। যদি পাঁচ মিনিট দরকার হয় তাহলে তারা একটা সুইচ টিপ দিয়ে বসে থাকবেন, আর যদি অনেক পানি থাকে এবং সেটি গরম করার জন্য পাঁচ, দশ মিনিট পর্যাপ্ত না হয়, তাহলে তারা পনেরো মিনিটের সুইচটি চেপে অন্য কাজে মন দিতে পারবেন-কাজ শেষ হলে এটি নিজে নিজেই বন্ধ হয়ে আমাদের জানান দিবে। রায়হানের স্যার রায়হানকে দায়িত্ব দিলেন সার্কিট তৈরি করে সেটির কার্যক্রম পরীক্ষা করে দেখতে। রায়হান মোটামুটি একটা উপায়ের কথা চিন্তা করে একটা সার্কিট তৈরি করলেন। ব্রেড বোর্ডে সেটি লাগানো হলো। তারপর দেখা গেল, ঠিক পাঁচ, দশ, পনেরো মিনিটের টাইমিং সার্কিট না হলেও মোটামুটি কাজ চালানোর মতো হয়েছে। স্যারকে সেটা দেখানো মাত্র উনি একটি মুচকি হাসি উপহার দিলেন। কারণ রায়হানের সার্কিটটা কাজ করলেও পুরা সিস্টেমটি বিশাল আকার ধারণ করেছে, অসংখ্য ক্যাপাসিটর, রেজিস্টেন্সের সমন্বযে। এই নকশায় টাইমার সার্কিট তৈরি করলে সেটা মোটামুটি মশা মারতে কামান দাগার মতো খরচের ব্যাপার হয়ে যাবে। তারপর স্যার নিজেই কাগজ কলম দিয়ে একটা চমৎকার ডিজাইন এঁকে দিলেন। সেই সিস্টেমে মাথা খাটানো হয়েছে বেশি, তাই খরচ কমে গিয়েছে, মূল যন্ত্রটি সরল এবং রায়হানের যন্ত্রের চেযেও দক্ষ হয়েছে। স্যারও একজন ইঞ্জিনিয়ার, রায়হানও ছিলেন তাই। কিন্তু রায়হানের সাথে তার পার্থক্য হচ্ছে স্যার ছিলেন দক্ষ আর রায়হান ছিলেন শিক্ষানবিশ। তিনি এমনভাবে একটি সিস্টেমের ডিজাইন করতে সক্ষম যেটার খরচ কম হবে, অপ্রয়োজনীয় জিনিসে ভরপুর থাকবে না, সর্বোপরি সবচেয়ে ভালো কাজ করবে। এতদিন আমরা ঈশ্বরকে রায়হানের স্যারের মতোই চৌকস ডিজাইনার বলে মনে। করতাম। কিন্তু এখন নিবিড় পর্যবেক্ষণে দেখা গেল তিনি তা নন। প্রকৃতিতে তার হাতে যেসব জিনিসপত্র ছিল তা দিয়ে তিনি চাইলে আরও সুনিপুণ নকশা করতে পারতেন। অপরদিকে বিবর্তন জ্ঞানে আমরা জানি, প্রকৃতিতে বিভিন্ন প্রাণীদেহের এক অঙ্গ বিবর্তনের পথ ধরে অন্য অঙ্গে পরিবর্তিত হয়েছে। এভাবে পরিবর্তিত হলে স্বাভাবিকভাবেই কিছু সমঝোতা করা আবশ্যক। প্রকৃতি জুড়ে আমরা তাই সুনিপুণ ডিজাইনের পরিবর্তনে অসংখ্য সমঝোতা দেখতে পাই। যেহেতু আমাদের অজ্ঞতার সুযোগে স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণের হাতিয়ার হিসেবে এতদিন ‘আর্গুমেন্ট ফ্রম ডিজাইন ব্যবহৃত হয়ে আসছিল, তাই সেটির অনুকরণে বিবর্তন হওয়ার প্রমাণ হিসেবে এসেছে আমাদের আর্গুমেন্ট ফ্রম ব্যাড ডিজাইন!
ছবি। পেজ ১০৮
চিত্র : মানবদেহের বিভিন্ন ভুল নকশার উদাহরণ
প্রজাতির ডিজাইনের ত্রুটি নিয়ে আলোচনায় সবার আগেই আসবে স্তন্যপায়ী প্রাণীদের বাকযন্ত্রের স্নায়ুর (Recurrent Laryngeal Nerve) কথা। মস্তিষ্ক থেকে বাযন্ত্র পর্যন্ত আবর্তিত এই স্নাযুটি আমাদের কথা বলতে এবং খাবার হজম করতে সাহায্য করে। মানুষের ক্ষেত্রে এই স্নায়ুর মস্তিষ্ক থেকে বাকযন্ত্র পর্যন্ত আসতে এক ফুটের মতো দূরত্ব অতিক্রম করা প্রযোজনা কিন্তু কৌতূহল উদ্দীপক ব্যাপার হলো, এটি সরাসরি মস্তিষ্ক থেকে বাকযন্ত্রে যাওয়ার রাস্তা গ্রহণ করে নি। মস্তিষ্ক থেকে বের হয়ে এটি প্রথমে চলে যায় বুক পর্যন্ত। সেখানে হৃৎপিণ্ডের বাম অলিন্দের প্রধান ধমনি এবং ধমনি থেকে বের হওয়া লিগামেন্টকে পেঁচিয়ে আবার উপরে উঠতে থাকে। উপরে উঠে তারপর সে যাত্রাপথে ফেলে আসা বাকযন্ত্রের সাথে সংযুক্ত হয়। হাত মাথার পেছন দিয়ে। ঘুরিয়ে ভাত খাওয়ার ব্যাপারের মতো এই যাত্রাপথে স্নায়ুটি তিন ফুটের চেয়েও বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে। স্তন্যপায়ী জিরাফের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। মস্তিষ্ক থেকে বের হয়ে সে লম্বা গলা পেরিয়ে বুকের মধ্যে ঘোরাঘুরি শেষে আবার লম্বা গলা পেরিয়ে উপরে উঠে বাকযন্ত্রে সংযুক্ত হয়। সরাসরি সংযুক্ত হলে যে দূরত্ব তাকে অতিক্রম করতে হতো, তার থেকে প্রায় পনেরো ফুট বেশি দূরত্ব সে অতিক্রম করে।
বাকযন্ত্রের স্নায়ুর এই আবর্তিত পথ শুধু খুব বাজে। ডিজাইনই নয়, এটি ভয়ংকরও। স্নাযুটির এই অতিরিক্ত দৈর্ঘ্যের কারণে এর আঘাত পাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে। ধরা যাক, কেউ আপনাকে বুকে আঘাত করল। এই বস্তুটির বুকে থাকার কথা ছিল না, কিন্তু আছে এবং যার কারণে ঠিকমতো আঘাত পেলে আমাদের গলার স্বর বন্ধ হয়ে আসে। যদি কেউ বুকে ছুরিকাহত হয় তাহলে কথা বলার ক্ষমতা নষ্টের পাশাপাশি খাবার হজম করার ক্ষমতাও ধ্বংস হয়ে যায়। বোঝা যায় কোনো মহাপরিকল্পক এই স্নায়ুটির ডিজাইন করেন নি, করলে তিনি এই কাজ করতেন না। তবে স্নায়ুর এই অতিরিক্ত ভ্রমণ বিবর্তনের কারণে আমরা যা আশা করি ঠিক তাই।
মানুষ তথা স্তন্যপায়ীদের বাকযন্ত্রের এই চক্রাকার পথ আমরা যে মাছের মতো প্রাণী হতে বিবর্তিত হয়েছি তার এক চমৎকার প্রমাণ। মাছের শরীরের নাড়ি-ভুঁড়ি ঢেকে রাখার কাঠামোর ষষ্ঠ শাখাঁটি (6th branchial arch) ফুলকায় রূপান্তরিত হয়েছিল। ফুলকায় রক্ত সরবরাহ করত হৃদপিণ্ডের বাম দিকের প্রধান ধমনির দ্বিতীয় ভাগ যা Aortic Arch নামে পরিচিত। এই ধমনির পেছনে ছিল ভেগাস স্নায়ুর (Vagus Nerve) চতুর্থ শাখা। প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেকটা মাছের ফুলকা সামগ্রিকভাবে এগুলো নিয়েই ছিল। স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রে মাছের নাড়ি-ভুঁড়ি ঢেকে রাখার ষষ্ঠ শাখার একটি অংশ বিবর্তিত হয়ে বাকযন্ত্রে রূপান্তরিত হয়েছিল। সেই সময় যেহেতু ফুলকাই বিলুপ্ত, সুতরাং ফুলকাকে রক্ত সরবরাহকারী, হৃদপিণ্ডের বামদিকের প্রধান ধমনির প্রয়োজনীয়তা শেষ হয়ে গিযেছিল। কাজ না থাকায় এটি মূল গঠন থেকে একটু নিচে নেমে বুকের কাছে চলে এসেছিল। আর যেহেতু এই ধমনির পেছনে ছিল স্নায়ুটি, তাই একেও বাধ্য হয়ে নেমে যেতে হয়েছিল বুকের দিকে। তারপর বুকে থাকা বাম অলিন্দের প্রধান ধমনি এবং ধমনি থেকে বের হওযা লিগামেন্টকে প্যাঁচানো শেষ করে সে আবার উপরে উঠে এসে বিবর্তিত বাকযন্ত্রের সাথে সংযুক্ত হয়েছিল। বাকযন্ত্রের স্নায়ুর অতিরিক্ত ভ্রমণের কারণ এটাই। বোঝা গেল, বাকযন্ত্রের স্নায়ুর এই চক্রাকার ভ্রমণ কোনো মহাপরাক্রমশালীর সৃষ্টিকর্তার ইঙ্গিতের পরিবর্তে বলছে আমাদের পূর্বপুরুষদের কথা।
ছবি। পেজ ১১০
চিত্র : সায়েন্টিফিক আমেরিকানের ২০০১ সালের মার্চ সংখ্যায় মানবদেহের বিভিন্ন দুর্বল ডিজাইন নিয়ে আলোচনা করা হয়।
এই লেখার শুরুতেই প্যালের করা মানব দেহের সাথে ঘড়ির তুলনা সম্পর্কে আমরা জেনেছি। যুক্তিগত ফ্যালাসি আক্রান্ত এই তুলনার মাধ্যমে অনেক মানুষকে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হলেও সত্যিকার অর্থে মানব দেহের সাথে ঘড়ির কোনো ধরনের তুলনাই হয় না। সায়েন্টিফিক আমেরিকায় প্রকাশিত ‘If Humans Were Built to Last প্রবন্ধে লেখক এলশ্যাকি, কেয়ার্নস এবং বাটলার মানব দেহের বিভিন্ন ব্যাড ডিজাইন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন[৮৬]। শুধু তাই নয়, একজন দক্ষ প্রকৌশলবিদের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা সেসমস্ত ডিজাইনজনিত ত্রুটি বিচ্যুতিগুলোর সমাধান দিয়ে বলেছেন, এভাবে ত্রুটিগুলো সারিয়ে নিতে পারলে সবারই একশ বছরের বেশি দীর্ঘ জীবন লাভ সম্ভব। প্রবন্ধটি থেকে কিছু উদাহরণ হাজির করার লোভ সামলাতে পারছি না। দেখা গেছে আমাদের দেহে ত্রিশ বছর গড়াতে না গড়াতেই হাড়ের ক্ষয় শুরু হয়ে যায়। যার ফলে হাড়ের ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি পায়, একটা সময় অস্টিওপরোসিসের মতো রোগের উদ্ভব হয়। আমাদের বক্ষপিঞ্জরের যে আকার তা দেহের সমস্ত অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট নয়। শুধু হাড় নয়, আমাদের দেহের মাংসপেশিও যথেষ্ট ক্ষয়প্রবণ। বয়সের সাথে সাথে আমাদের পায়ের রগগুলোর বিস্তৃতি ঘটে, যার ফলে প্রায়শই পাযের শিরা ফুলে ওঠে। সন্ধিস্থল বা জয়েন্টগুলোতে থাকা লুব্রিকেন্ট পাতলা হয়ে সন্ধিস্থলের ক্ষয় স্বরান্বিত করে। পুরুষের প্রোস্টেট গ্ল্যান্ড সময়ের সাথে সাথে বৃদ্ধি পেয়ে প্রস্রাবের ব্যাঘাত ঘটায়।
ওলশ্যাঙ্কি, কোর্নস এবং বাটলার প্রবন্ধটিতে দেখিয়েছেন ত্রুটি বিচ্যুতিগুলো দূর করার পর ‘পারফেক্ট ডিজাইনের অধিকারী মানবদেহের চেহারা ঠিক কী রকম হতে পারে। এধরনের দেহে থাকবে বিরাট কান, তারসংযুক্ত চোখ, বাঁকানো কাঁধ, সামনের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়া কবন্ধ, ক্ষুদ্রকায় বাহু এবং কাঠামো, সন্ধিস্থলের চারিদিকে অতিরিক্ত আস্তরণ বা প্যাডিং, অতিরিক্ত মাংসপেশি, পুরু স্পাইনাল ডিস্ক, রিভার্সড হাঁটুর জয়েন্ট ইত্যাদি। তিনি হয়ত আমাদের বর্তমান তথাকথিত ‘সৌন্দর্যের স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ভুবনমোহিনী প্রিয়দর্শিনী হিসেবে বিবেচিত হবেন না, কিন্তু শতায়ু হওয়ার জন্য সঠিক কাঠামোর অধিকারী হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতেই পারেন।
মন্দ ও ত্রুটিপূর্ণ নকশার উদাহরণ আরও অনেক আছে। মহিলাদের জননতন্ত্র প্রাকৃতিকভাবে এমনভাবে বিবর্তিত হয়েছে যে অনেকসময়ই নিষিক্ত শার্ম ইউটেরাসের বদলে অবাঞ্ছিতভাবে ফ্যালোপিয়ান টিউব, সার্ভিক্স বা ওভারিতে গর্ভসঞ্চার ঘটায়। এ ব্যাপারটিকে বলে ‘একটোপিক প্রেগন্যান্সি। ওভারি এবং ফ্যালোপিয়ান টিউবের মধ্যে অতিরিক্ত একটি গহ্বর থাকার ফলে এই ধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। এটি মানবদেহে ‘ব্যাড ডিজাইনের চমৎকার একটি উদাহরণ। আগেকার দিনে এধরনের পরিস্থিতির উদ্ভব হলে শিশুসহ মাযের জীবন সংশয় দেখা দিত। এখন চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আগে থেকেই গর্ভপাত ঘটিয়ে মায়েদের জীবনহানির আশঙ্কা অনেকটাই কাটিয়ে তোলা গেছে।
ছবি। পেজ ১১৩
চিত্র : মানবদেহের বিভিন্ন দুর্বল ডিজাইন দূর করে শতায়ুর অধিকারী কাঠামো বানানো সম্ভব (সায়েন্টিফিক আমেরিকান, ২০০১ সালের মার্চ সংখ্যার সৌজন্যে)।
মানুষের ডিএনএ-তে ‘জাঙ্ক ডিএনএ’ নামের একটি অপ্রয়োজনীয় অংশ আছে যা আমাদের আসলে কোনো কাজেই লাগে না। ডিস্ট্রফিন জিনগুলো শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, সময় সময় মানবদেহে ক্ষতিকর মিউটেশন ঘটায়। ডিএনএ-র বিশৃঙ্খলা ‘হান্টিংটন ডিজিজের’-এর মতো বংশগত রোগ তৈরি করে। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমাদের গলায় মুখগহ্বর বা ফ্যারিংস এমনভাবে তৈরি যে একটু অসাবধান হলেই শ্বাসনালীতে খাবার আটকে আমরা হেঁচকি তুলি। এগুলো সবই প্রকৃতির মন্দ নকশার বা ‘ব্যাড ডিজাইনের উদাহরণ। গবেষকেরা দেখেছেন এমনকি আমাদের মানব-মস্তিষ্কও এই ধরণের ‘মন্দ নকশার বাইরে নয়[৮৭]।
ছবি। পেজ ১১৪
চিত্র : একটোপিক প্রেগন্যান্সি : মানবদেহের মন্দ নকশার আরেকটি উদাহরণ।
ব্যাড ডিজাইনের উদাহরণ শুধু জীববিজ্ঞানে নয়, জ্যোতির্বিদ্যাতেও দৃশ্যমান। বিশ্বাসীরা যদিও সবকিছুর পেছনেই ‘মানব সৃষ্টির সুমহান উদ্দেশ্য খোঁজার চেষ্টা করেন, তবে তাদের যুক্তি কোনোভাবেই ধোপে টেকে না। প্রাণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যদি মুখ্য হয়, তবে মহাবিস্ফোরণের পর ঈশ্বর কেন ৭০০ কোটি বছর লাগিয়েছিলেন এই পৃথিবী তৈরি করতে, আর তারপর আরও ৬০০ কোটি বছর লাগিয়েছিলেন মানুষের উন্মেষ ঘটাতে তার কোনো যৌক্তিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। এটি নিঃসন্দেহেই মন্দ নকশায়ন বা ব্যাড ডিজাইনের উদাহরণ। পৃথিবী সৃষ্টির ইতিহাসের পরিক্রমায় আমরা আজ জনি, মানুষ পুরো সময়ের একশ ভাগের এক ভাগেরও কম সময় ধরে পৃথিবীতে রাজত্ব করছে। তারপরও মানুষকে এত বড় করে তুলে ধরে মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করার কী প্রয়োজন? অথচ তথাকথিত মনুষ্যকেন্দ্রিক যুক্তির দাবিদারেরা তা করতেই আজ সচেষ্ট। আর তা ছাড়া প্রাণ কিংবা পরিশেষে মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই যদি মুখ্য হয়, তবে বলতেই হয় মহান সৃষ্টিকর্তা তার সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় সৃষ্টির চেয়ে অপচয়ই করেছেন বেশি। বিগব্যাং ঘটানোর কোটি কোটি বছর পর পৃথিবী নামক একটি সাধারণ গ্রহে প্রাণ সঞ্চার করতে গিয়ে অযথাই সারা মহাবিশ্ব জুড়ে তৈরি করেছেন হাজার হাজার, কোটি কোটি ছোট বড় নানা গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ-যারা আক্ষরিক অর্থেই আমাদের সাহারা মরুভূমির চেযেও বন্ধ্যা, ঊষর আর প্রাণহীন। শুধু কোটি কোটি প্রাণহীন নিস্তব্ধ গ্রহ-উপগ্রহ তৈরি করেই ঈশ্বর ক্ষান্ত হন নি, তৈরি করেছেন অবারিত শূন্যতা, গুপ্ত পদার্থ (Dark Matter) এবং গুপ্ত শক্তি (Dark Energy)-যেগুলো নিষ্প্রাণ তো বটেই, এমনকি প্রাণ সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্যের প্রেক্ষাপটে নিতান্তই বেমানান। আসলে এ ব্যাপারগুলোকেও বিবর্তনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার না করলে কোনো সমাধানে পৌঁছুনো যাবে না। আমরা যতই নিজেদের সৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে বসিয়ে সান্ত্বনা খোঁজার চেষ্টা করি না কেন, এই মহাবিশ্ব এবং এই পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভবের পেছনে আসলে কোনো ডিজাইন নেই, পরিকল্পনা নেই, নেই কোনো বুদ্ধিদীপ্ত সত্ত্বার সুমহান উদ্দেশ্য। প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানের জন-ধীশক্তি বিষয়ক বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক ড. রিচার্ড ডকিন্স সেটিকেই স্পষ্ট করেছেন নিচের ক’টি অসাধারণ পঙক্তিমালায় (সায়েন্টিফিক আমেরিকান, নভেম্বর, ১৯৯৫ : ৮৫)–
আমাদের চারপাশের বিশ্বজগতে বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলো দেখলেই বোঝা যায় এর মধ্যে কোনো পরিকল্পনা নেই, উদ্দেশ্য নেই, নেই কোনো শুভাশুভের অস্তিত্ব; আসলে অন্ধ, করুণাহীন উদাসীনতা ছাড়া এখানে আর কিছুই চোখে পড়ে না।
.
আদম-হাওয়া ও নুহের মহাপ্লাবন
একটা খুব প্রিয় একটা উদ্ধৃতি দিয়ে শুরু করি। ইউটিউবে এক ব্লগার নিজের পাতায় লিখে রেখেছিলেন কথাটি– ‘সত্য কখনোই কাউকে আঘাত করে না, যদি না সেখানে আগে থেকেই একটা মিথ্যা অবস্থান করে। বিবর্তনের জন্য কথাটি গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫৯ সালে ডারউইন এবং ওয়ালেস যখন বিবর্তন তত্বটি প্রকাশ করেন তখন চার্চের বিশপের স্ত্রী আর্তনাদ করে বলেছিলেন[৮৮]–
বনমানুষ থেকে আমাদের বিবর্তন ঘটেছে। আশা করি সেটা যেন কখনোই সত্য না হয়। আর যদি তা একান্তই সত্য হয়ে থাকে তবে চলো আমরা সবাই মিলে প্রার্থনা। করি সাধারণ মানুষ যেন কখনোই এই কথা জানতে না পারে।
যে প্রশ্নের উত্তর আমাদের জানা নেই সেই প্রশ্নগুলোর মনগড়া উত্তর দেওয়া এবং তা মানুষকে বিশ্বাস করানোই ধর্মের কাজ। বিবর্তনের ফলে প্রজাতির ক্রমবিকাশ হয়েছে, এই কথা মানুষ জানতে পেরেছে দুই শতকও হয় নি। উত্তরটা যদিও একেবারে নতুন কিন্তু প্রশ্নটা নয়। তাই দীর্ঘসময় ধরে মানুষ নানা উত্তর কল্পনা করে নিয়েছে। আর ধর্ম এসে সেই উত্তরগুলোকে খোদার উত্তর বা খোদা থেকে প্রাপ্ত উত্তর বলে। প্রতিষ্ঠিত করেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ধর্মগুলো ইহুদি, খ্রিস্টান এবং মুসলমানদের বিশ্বাস করা সৃষ্টিবাদ সেরকমই একটি জিনিস। বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থের লাইন উদ্ধৃত করে লেখাটা দীর্ঘ করব না, কারণ মূল কাহিনি আমাদের কমবেশি সবারই জানা। বর্ণনাভেদে ধর্মগ্রন্থগুলোতে পার্থক্য থাকলেও মূল কাহিনি মোটামুটি একইরকম এবং এই দুই ক্ষেত্রেই সৃষ্টিবাদ দুটি অংশে বিভক্ত।
১। আল্লাহ প্রথম মানুষ হিসেবে আদমকে সৃষ্টি করেছিলেন। তার পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল বিবি হাওয়াকে। অতঃপর শয়তানের প্ররোচনায় ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করায় তাদের বেহেশত থেকে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করা হয়। তারপর তাদের থেকেই সৃষ্টি হয় মানব সভ্যতা। (জেনেসিস ১), কোরআন-আল-আরাফ ৭: ১৮৯, আল-ইমরান ৩ : ৫৯, আল-আরাফ ৭: ১১-২৭।
২। মানব সভ্যতার এক পর্যায়ে নুহ নবীর সময়ে পৃথিবীর সকল মানুষ পাপে নিমজ্জিত হয়, ভুলে যায় ঈশ্বরকে। ঈশ্বর ক্রোধান্বিত হয়ে নুহকে একটি নৌকা বানানোর হুকুম দেন। সেই নৌকায় নির্বাচিত কয়েকজন মানুষ এবং পৃথিবীর সকল ধরনের প্রজাতির এক জোড়া তুলে নেওয়া হয়। বাকিদের। মহাপ্লাবনের মাধ্যমে ধ্বংস করা হয়। পাপের দাযে ধ্বংস করা হয় মহাপ্লাবনের আগের রাতে জন্মগ্রহণ করা শিশুকেও। (জেনেসিস ৭-৪)
এই ঈশ্বর ইব্রাহিমের ঈশ্বর বা গড অব আব্রাহাম। পৃথিবীর প্রধান তিনটি ধর্ম এই ঈশ্বরের পূজারী। বিবর্তন বিজ্ঞানী এবং এর লেখকরা বিবর্তন এবং নানা ধরনের সূক্ষ সূক্ষ ব্যাপার নিয়ে অসংখ্য বই, নিবন্ধ লিখলেও এই সৃষ্টিবাদকে অযৌক্তিক ব্যাখ্যা করতে খুব একটি সময় দেন নি। কিন্তু সময় দেওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাদের কাছে। এটি একটি পৌরাণিক কাহিনি হলেও পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ আক্ষরিকভাবে এ গল্পে বিশ্বাস করে। যা তাদের মনের কপাট বন্ধ করে রাখে ফলে বিবর্তনের হাজারো প্রমাণ তাদের মাথায় ঢোকে না।
ধর্মগ্রন্থে আমরা আদম হাওয়ার কথা পড়েছি, পড়েছি তাদের দুই সন্তান হাবিল, কাবিলের কথা। তবে আমাদের পড়াশোনা ঠিক এখানেই শেষ, আমরা ধরে নিয়েছি দুটো মানুষ, তাদের সন্তানরা মিলে সারা পৃথিবী মানুষে মানুষে ছেয়ে ফেলেছে। তবে এখানেই থেমে না গিয়ে আরেকটু সামনে আগালে, আরেকটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই একটা গভীর প্রশ্নের সম্মুখীন আমাদের হতে হ্যাঁ সন্তান উৎপাদনটা ঠিক কীভাবে হলো?
গুগল ডিকশনারি ইনসেস্ট বা অজাচার-এর অর্থ বলছে এটি ভাই-বোন, পিতা-কন্যা, মাতা-ছেলের মধ্যে যৌন সঙ্গমের দরুন একটি অপরাধ। ধর্ম নিজেকে নৈতিকতার প্রশাসন হিসেবে পরিচয় দেয়, অথচ তারা আমাদের যে গল্প শোনায় তা মারাত্মক রকমের অনৈতিক। আদম হাওয়ার গল্প সত্যি হয়ে থাকলে পৃথিবীতে আমরা এসেছি মারাত্মক এক পাপের মধ্য দিয়ে।
পাপ-পুণ্যের কথা থাক। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটি বিবেচনা করা যাক। ইনসেস্ট বা অজাচারকে বৈজ্ঞানিকভাবে অভিহিত করা হয়ে থাকে ইন-ব্রিডিং হিসেবে। নারী ও পুরুষের আত্মীয় হওয়া মানে তাদের মধ্যে জেনেটিক গঠনে পার্থক্য কম। এখন তারা যদি একে অন্যের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে সন্তান উৎপাদন করে তাহলে সেই সন্তানের মধ্যে ব্যাড মিউটেশনের সম্ভাবনা প্রবল। এর ফলে। সন্তানটি বেশিরভাগ সময়ই হবে বিকলাঙ্গ। আর এই কারণেই প্রকৃতিতে আমরা ইন-ব্রিডিং দেখতে পাই না। কারণ ইন ব্রিডিং হলে প্রজাতির টিকে থাকার সম্ভাবনা কমে যায়, তারা খুব দ্রুত প্রকৃতি থেকে হারিয়ে যাবে। কিন্তু যদি ভিন্ন পরিবার থেকে এসে দুইজন সন্তান উৎপাদন করে তাহলে সন্তানের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ জেনেটিক ভ্যারিয়েশন হবে। আর যথেষ্ট পরিমাণ জেনেটিক ভ্যারিয়েশন প্রজাতির টিকে থাকার জন্য অবশ্য দরকার। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে পৃথিবীর চিতাবাঘের সংখ্যা নেমে এসেছিল প্রায় ত্রিশ হাজারে। সংখ্যার দিক থেকে বিবেচনা করলে ত্রিশ হাজার একটি বড় সংখ্যা হলেও জনপুঞ্জের জনসংখ্যা হিসাব করলে তা খুব একটা বড় নয়। আর এই কারণেই চিতাবাঘকে ইনব্রিডিং এর আশ্রয় নিতে হয়েছিল। যার পরিণামে আজকে আমরা দেখতে পাই, প্রকৃতিতে চিতাবাঘ বিলুপ্ত প্রায়। সুতরাং দুইটি মানুষ থেকে সমগ্র মানব জাতির সৃষ্টি হয়েছিল, এর মতো হাস্যকর কথা আর নেই। পৃথিবীতে কখনোই আদম, হাওয়া নামে দুইটি মানুষ ছিল না।
এবার আসা যাক নুহের মহাপ্লাবন নিয়ে। সিলেট থেকে প্রকাশিত যুক্তি পত্রিকার সম্পাদক এবং ২০০৬ সালে মুক্তমনা। র্যাশনালিস্ট অ্যাওয়ার্ড পাওয়া অনন্ত বিজয় দাশ ‘মহাপ্লাবনের বাস্তবতা’ নামে একটি সুলিখিত প্রবন্ধে বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থে বর্ণিত নুহের মহাপ্লাবন সম্পর্কিত আয়াত লিপিবদ্ধ করেছেন। আলোচনার সুবিধার্থে সেখান থেকে কয়েকটি তুলে ধরা হলো[৮৯]।
ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল-এর ওল্ড টেস্টামেন্টের (পুরাতন নিয়ম) অন্তর্গত তৌরাত শরিফে হযরত নুহ (আঃ) সম্পর্কে বলা হয়েছে–
এই অবস্থা দেখে ঈশ্বর নোয়াকে বললেন, ‘গোটা মানুষ জাতটাকেই আমি ধ্বংস করে ফেলব বলে ঠিক করেছি। মানুষের জন্যই দুনিয়া জোরজুলুমে ভরে উঠেছে। মানুষের সঙ্গে দুনিয়ার সবকিছুই আমি ধ্বংস করতে যাচ্ছি। তুমি গোফর কাঠ দিয়ে তোমার নিজের জন্য একটা জাহাজ তৈরি করো। তার মধ্যে কতগুলো কামরা থাকবে; আর সেই জাহাজের বাইরে এবং ভেতরে আলকাতরা দিয়ে লেপে দিবে। জাহাজটা তুমি এইভাবে তৈরি করবে; সেটা লম্বায় হবে তিনশো হাত, চওড়ায় পঞ্চাশ হাত, আর উচ্চতা হবে ত্রিশ হাত। জাহাজটার ছাদ থেকে নিচে এক হাত পর্যন্ত চারিদিকে একটা খোলা জায়গা রাখবে আর দরজাটা হবে জাহাজের একপাশে। জাহাজটাতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলা থাকবে। আর দেখ, আমি দুনিয়াতে এমন একটা বন্যার সৃষ্টি করব যাতে আসমানের নিচে যেসব প্রাণী শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছে তারা সব ধ্বংস হয়ে যায়। দুনিয়ার সমস্ত প্রাণীই তাতে মারা যাবে।’ (পয়দায়েশ, ৬ : ১৩-১৭)।
‘কিন্তু আমি তোমার জন্য আমার ব্যবস্থা স্থাপন করব। তুমি গিয়ে জাহাজে উঠবে আর তোমার সঙ্গে থাকবে তোমার ছেলেরা, তোমার স্ত্রী ও তোমার ছেলেদের স্ত্রী। তোমার সঙ্গে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য তুমি প্রত্যেক জাতের প্রাণী থেকে স্ত্রী পুরুষ মিলিযে এক এক জোড়া করে জাহাজে তুলে নেবে। প্রত্যেক জাতের পাখি, জীবজন্তু ও বুকে-হাঁটা প্রাণী এক এক জোড়া করে তোমার কাছে আসবে যাতে তুমি তাদের বাঁচিয়ে রাখতে পারো; আর তুমি সব রকমের খাবার জিনিস জোগাড় মজুদ করে রাখবে। সেগুলোই হবে তোমার ও তাদের খাবার। নুহ তা-ই করলেন। ঈশ্বরের হুকুমমতো তিনি সবকিছুই করলেন।’ (পয়দায়েশ, ৬ : ১৮-২২)।
.
কোরআন শরিফে হযরত নুহ এবং মহাপ্লাবন সম্পর্কে বর্ণিত তথ্য
‘অতঃপর আমি তার কাছে ওহি পাঠালাম যে, তুমি আমার তম্বাবধানে আমারই ওহি অনু্যায়ী একটি নৌকা প্রস্তুত করো। তারপর যখন আমার (আজাবের) আদেশ আসবে এবং (জমিনের) চুল্লি প্লাবিত হয়ে যাবে, তখন (সবকিছু থেকে) এক এক জোড়া করে নৌকায় উঠিয়ে নাও, তোমার পরিবার পরিজনদেরও (উঠিয়ে নেবে, তবে তাদের মধ্যে যার ব্যাপারে আল্লাহতায়ালার সিদ্ধান্ত এসে গেছে সে ছাড়া। (দেখো), যারা জুলুম করেছে তাদের ব্যাপারে আমার কাছে কোনো আরজি পেশ করো না, কেননা (মহাপ্লাবনে আজ) তারা নিমজ্জিত হবেই’ (সুরা আল মোমেনুন, ২৩ : ২৭)।
‘তুমি আমারই তত্বাবধানে আমারই ওহির আদেশে একটি নৌকা বানাও এবং যারা জুলুম করেছে, তাদের ব্যাপারে তুমি আমার কাছে কোনো আবেদন নিয়ে) হাজির হয়ো না, নিশ্চয়ই তারা নিমজ্জিত হবে’ (সুরা হুদ, ১১ : ৩৭)।
‘(পরিকল্পনা মোতাবেক) সে নৌকা বানাতে শুরু করল। যখনই তার জাতির নেতৃস্থানীয় লোকেরা তার পাশ দিয়ে আসা-যাওয়া করত, তখন (নুহকে নৌকা বানাতে দেখে) তাকে নিয়ে হাসাহাসি শুরু করে দিতো; সে বললো (আজ) তোমরা যদি আমাদের উপহাস করো (তাহলে মনে রেখো), যেভাবে (আজ) তোমরা আমাদের ওপর হাসছো (একদিন) আমরাও তোমাদের ওপর হাসবো’ (সুরা হুদ, ১১ : ৩৮)।
‘অবশেষে (তাদের কাছে আজাব সম্পর্কিত) আমার আদেশ এসে পৌঁছাল এবং চুলো থেকে একদিন পানি) উথলে উঠলো, আমি (নুহকে) বললাম, (সম্ভাব্য) প্রত্যেক জীবের (পুরুষ-স্ত্রীর) এক একজোড়া এতে উঠিয়ে নাও, (সাথে) তোমার পরিবার-পরিজনদেরও (ওঠাও) তাদের বাদ দিয়ে, যাদের ব্যাপারে আগেই সিদ্ধান্ত (ঘোষিত) হয়েছে এবং (তাদেরও নৌকায় উঠিয়ে নাও) যারা ঈমান এনেছে; (মূলত)। তার সাথে (আল্লাহর ওপর) খুব কমসংখ্যক মানুষই ঈমান এনেছিল’ (সুরা হুদ, ১১ : ৪০)।
নুহের মহাপ্লাবন সম্পর্কিত পৌরাণিক গল্পের সূচনা এই ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে নয়। এই গল্পের শেকড় খুঁজতে গিয়ে আমরা সবচেয়ে পুরাতন যে ভাষ্য বা বর্ণনা পাই সেটা ২৮০০ খ্রিস্টপূর্ব সময়কার ঘটনা। সুমেরিয়ান পুরাণে এমন এক বন্যার বর্ণনা পাওয়া যায় যার নায়ক ছিল রাজা জিউশুদ্র, যিনি একটি নৌকা তৈরির মাধ্যমে একটি ভয়ংকর প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে অনেককে রক্ষা করেছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ থেকে ১৪০০-এর মধ্যে বিখ্যাত ব্যাবেলনিয়ান পৌরাণিক চরিত্র গিলগামেশ তার এক পুরুষের যুতনাপিসটিমের কাছ থেকে একই রকম এক বন্যার কথা। শুনতে পান। সেই গল্পানুসারে পৃথিবীর দেবতা আ (Ea) রাগান্বিত হয়ে পৃথিবীর সকল জীবন ধ্বংস করে ফেলার অভিপ্রাযের কথা যুতনাপিসটিমকে জানান। তিনি যুতনাপিসটিমকে ১৮০ ফুট লম্বা, সাততলা বিশিষ্ট এবং প্রতিটি তলায় নয়টি কক্ষ থাকবে এমন একটি নৌকা তৈরি করে তাতে পৃথিবীর সকল প্রজাতির এক জোড়া করে তুলে নেওয়ার আদেশ দেন[৯০]।
গিলগামেশের এই মহাপ্লাবন মিথটিই লোকে মুখে সবচেয়ে বেশি ছড়িয়ে পড়ে। আব্রাহামিক গডের আবিষ্কারক এবং পূজারী হিব্রুরা প্যালেস্টাইনে আসার অনেক আগে থেকেই সেখানকার মানুষদের কাছে এই গল্প প্রচলিত ছিল। আর সেই গল্পের প্রভাবই আমরা দেখতে পাই, পরবর্তীকালে হিব্রুদের গড অব আব্রাহামের বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ তৌরাত, বাইবেলে। আর এই তৌরাত, বাইবেলের গল্প থেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছে আরবের ইসলাম ধর্মের কোরআনের নুহের মহাপ্লাবন কাহিনি।
একটা সংস্কৃতিকে এর ভৌগোলিক অবস্থান বেশ প্রভাবিত করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, একটি সংস্কৃতি যাদের ভৌগোলিক অবস্থান নদ-নদী বিধৌত, যেগুলো প্রায়শই বন্যা ঘটিযে জনপদ গিলে ফেলে, সেসব সংস্কৃতিতে নদ-নদী সম্পর্কিত কিংবা বন্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন গল্প চালু থাকে। সুমেরীয় এবং ব্যাবেলনীয় জনপদ টাইগ্রিস এবং ইউফ্রাটিস নদী দিয়ে আবৃত ছিল। এসব অঞ্চলে প্রায়শই বন্যা হতো। এখন এর মানে কি এই তৌরাত, বাইবেল, কোরআনের সকল গল্প মিথ্যা? অবশ্য এই প্রশ্ন করা মানেই পৌরাণিক কাহিনির সত্যিকারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করা। জোসেফ ক্যাম্পবেল (১৮৮৮, ১৯৪৯) তার সারাজীবন অতিবাহিত করেছেন এই বৈশিষ্ট্য সঠিকভাবে মানুষের কাছে ব্যাখ্যা করতে[৯১]। তার মতে, মহাপ্লাবন সম্পর্কিত পৌরাণিক কাহিনিগুলোকে আমরা যেভাবে দেখি তার থেকে এর অনেক গভীর মর্মার্থ রয়েছে। পৌরাণিক কাহিনি কোনো ঐতিহাসিক সত্য কাহিনি নয়, এটি হলো মানব সভ্যতার প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার সংগ্রাম। প্রতিটা মানুষের মনেই তার জন্মের উদ্দেশ্য, সে কীভাবে এল, কেমন করে এল এমন প্রশ্ন ঘুরে ফিরে আর এই প্রশ্ন থেকে মুক্তি পেতে সে বিভিন্ন উত্তর দাঁড করায়। আর তা থেকেই জন্ম নেয় পৌরাণিক কাহিনির পৌরাণিক কাহিনির সাথে বিজ্ঞানের বিন্দুমাত্র কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু ধর্ম এসে এই শাশ্বত কাহিনিগুলোকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গিযে একে বিজ্ঞান বলে প্রচার করেছে। এটা বিজ্ঞান এবং পৌরাণিক কাহিনি দুটির জন্যই অপমানজনক। সৃষ্টিবাদীরা পৌরাণিক কাহিনির চমৎকার সব গল্পকে গ্রহণ করেছে, তারপর সেটাকে ধ্বংস করেছে।
পৌরাণিক কাহিনিকে বিজ্ঞানে রূপান্তর করার আহাম্মকির উদাহরণ দিতে গেলে নুহের মহাপ্লাবনই যথেষ্ট। ৪৫০ (৭৫x৪৫) বর্গফুটের একটি নৌকায় কয়েক কোটি প্রজাতিকে জায়গা দিতে হবে। তাদের খাবারের ব্যবস্থা কী হবে? প্যঃনিষ্কাশন, পানি? ডায়নোসররা কোথায় থাকবে, কিংবা সামুদ্রিক প্রাণীরা। এক প্রাণীর হাত থেকে অন্য প্রাণীকে রক্ষার উপায় কী? ডাঙার প্রাণীরা যাওবা গেল, সমুদ্রে বসবাসরত প্রাণীরা বন্যায় মারা যাবে কেন আর কীভাবে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর বিশ্বাসীদের কাছে একটাই। ঈশ্বর চাইলে সব হবে। তবে সেক্ষেত্রে ঈশ্বরের নুহকে দিয়ে নৌকা বানিয়ে হাত ঘুরিয়ে ভাত খাওয়ার দরকার কী ছিল? তিনি চাইলে তো এক হুকুমেই পৃথিবীর তাবৎ পাপীকে মেরে ফেলতে পারতেন। তাতে করে অন্তত আগের দিন জন্ম নেওয়া নিষ্পাপ শিশুগুলো বেঁচে যেতো।
ছবি। পেজ ১১০
চিত্র : ক্যালিফোর্নিয়ায় অবস্থিত ইন্সটিটিউট অফ ক্রিয়েশন রিসার্চ মিউজিয়ামে নুহের নৌকার ছবি। মানুষকে জোর করে গালগল্প বিশ্বাস করানোর জন্য আলাদা আলাদা কম্পার্টমেন্টের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক উত্তরদানের চেষ্টা (!!) করা হয়েছে। ছবি সূত্র: বার্নাড লে কাইন্ড জে।
নৌকার কথা বাদ দিলেও বৈজ্ঞানিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে পৃথিবীতে এমন কোনো মহাপ্লাবন হয় নি, যাতে করে বাড়ি ঘর থেকে শুরু করে সকল উঁচু পর্বত ডুবে গিয়েছিল। এছাড়া মহাপ্লাবন হলে মৃত প্রাণীদের জীবাশ্মগুলো সব মাটির একই স্তরে থাকার কথা ছিল (যেহেতু তারা সবাই একই সময়ে মৃত্যুবরণ করেছে) তেমন প্রমাণও খুঁজে পান নি ভূ তত্ববিদরা। দেখা যাচ্ছে সৃষ্টিবাদীরা শুধু বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানকে অস্বীকার করছেন না, তারা অস্বীকার করছেন পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, ইতিহাস, ভূ-তত্ব, ফসিল বিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যাসহ সকল বিষয়কে।
নুহের মহাপ্লাবনের অসাড়তা আব্রাহামিক গডকে বেশ বিড়ম্বনায় ফেলে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এমন ঘটনা যেহেতু কোনোদিনও ঘটেনি এবং তিনি দাবি করেছেন ঘটেছে তাই আমরা সহজেই সিদ্ধান্তে আসতে পারি আব্রাহামিক গড বলে আসলে কেউ নেই, এটা মানুষের মন গড়া কল্পনা, ধর্মগ্রন্থগুলো মানুষের লিখিত।
.
স্বতঃ সংগঠন
ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন বা আইডি প্রবক্তারা তাদের বই, ডকুমেন্টারিতে সবসময় ৪০০ বিজ্ঞানীর একটি সম্মিলিত বিবৃতির উদাহরণ টানেন। তাদের মতে আইডিকে সমর্থন জানানোর জন্য বিজ্ঞানীরা এই বিবৃতি প্রদান করেছেন। এবার জানা যাক সত্যিকার অর্থেই এই বিজ্ঞানীরা তাদের সম্মিলিত বিবৃতিতে কী বলেছিলেন–
জীবনের জটিলতা ব্যাখ্যায়, আমরা র্যান্ডম মিউটেশন এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের সামর্থ্যের ব্যাপারে সন্দিহান। আমরা মনে করি যে প্রমাণগুলোর মাধ্যমে ডারউইন তত্ত্বের সঠিকতা নির্ধারণ করা হয়েছে সেগুলো আরও সূক্ষভাবে পরীক্ষা করা উচিত।[৯২]
লক্ষ্য করুন, এখানে একবারের জন্যও ‘ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন বা আইডি শব্দটা আসে নি। বিজ্ঞানীরা উপরে যে বিবৃতি দিয়েছেন তা নিতান্তই স্কেপটিক আচরণের শান্ত, সুকুমার অভিব্যক্তি, যৌক্তিক বিজ্ঞানমনস্ক আচরণ। তবে ডারউইনের তত্বকে নতুন করে আরও সূক্ষভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার আহ্বান-অপ্রয়োজনীয়, কেননা ডারউইনের বিগল যাত্রা পরবর্তী যে বিবর্তনীয় জীববিজ্ঞানের সূচনা হয়েছিল তার একমাত্র কাজই বিবর্তনের প্রমাণ পরীক্ষা নিরীক্ষা করা। ডারউইন তত্ত্বের মতো প্রতিনিয়ত অসংখ্য পরীক্ষা নিরীক্ষার সম্মুখীন অন্য কোনো তত্ত্বকে হতে হয় নি। গত দেড়শ বছর ধরে পরীক্ষা চলছে, চলবে অনন্তকাল।
এবার ৪০০ বিজ্ঞানীর উদ্ধৃতিতে ফিরে আসা যাক। একটা জিনিস উল্লেখ করা আবশ্যক, বিবর্তন প্রক্রিয়ায় র্যান্ডম মিউটেশন ও প্রাকৃতিক নির্বাচন ছাডা আরও বেশকিছু অত্যাবশ্যকীয় ব্যাপার কাজ করতে পারে। জীব, জড় দুই ধরনের জটিল বস্তু সংস্থান (Complex Material System) একটি প্রাকৃতিক ধর্ম প্রদর্শন করে যার নাম ‘স্বতঃ সংগঠন বা সেল অর্গানাইজেশন। স্বতঃ সংগঠন বলতে বিভিন্ন বস্তুর নানা ধরনের নকশায় বিন্যস্ত হওয়ার কথা বোঝানো হয়। আর গাণিতিক এই চমৎকার নকশা তৈরি হয় সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপায়ে, কোনো ধরনের মিরাকল বা অলৌকিকতা ব্যতীত।
‘Self-Made Tapestry’ নামের বইটিতে লেখক ফিলিপ বল বিভিন্ন জীব ও জড় বস্তুর প্রাকৃতিকভাবে নানা ধরনের নকশায় বিন্যস্ত হওয়ার উদাহরণ দেখিয়েছেন অসংখ্য চিত্র সহকারে। আশেপাশের বিভিন্ন জটিলতা দেখে সেগুলো ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ মনে করে তা নিয়ে পাগলামি করা সৃষ্টিবাদীদের পাগলামি রোধের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করতে পারে তার বইয়ে উল্লেখিত জটিলতাগুলো, যেগুলো একদমই নিজে নিজে প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হয়েছে[৯৩]। সত্যি কথা হলো, বিভিন্ন জীবিত জৈবতন্ত্রে সন্ধান পাওয়া নকশা একই সাথে জড সিস্টেমেও দেখতে পাওয়া যায় এবং এগুলো পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়নের মৌলিক সূত্র দিয়েই ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এদের কোনোটিই বাইরের কারও নিজের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য ব্যবহৃত অস্ত্র নয়। মনে রাখা দরকার, বিশ্বের প্রতিটি স্থানে কণাগুলো একে অপরের সাথে মিথস্ক্রিয়া করছে। এধরনের বিশ্বে সরলতা খুব সহজেই জটিলতার জন্ম দিতে পারে। পূর্ণ একটি ব্যবস্থা তার বিভিন্ন অংশের সমষ্টি ছাড়া কিছুই নয়[৯৪]।
প্রকৃতির প্রায় সকল জায়গায় ডাবল স্পাইরাল বিন্যাসের উপস্থিতিকে উদাহরণ হিসেবে নেয়া যাক[৯৫]। প্রকৃতিতে শতকরা ৮০ ভাগ উদ্ভিদ প্রজাতির ক্ষেত্রেই দেখা যায় কাণ্ড বা মধ্যরেখা থেকে পাতাগুলো উপরের দিকে কুণ্ডলাকারে বিস্তার লাভ করে। প্রতিটি পাতা তার নিচেরটি থেকে একটি নির্দিষ্ট কোণে অবস্থান করে উপর থেকে দেখলে, এধরনের কুণ্ডলাকার গড়নকে ডাবল স্পাইরাল তথা দ্বি-কুণ্ডলাকার মনে হয়। একটি পাতার মোচড় অন্যটার বিপরীত দিকে বলেই এমন গড়নের উদ্ভব ঘটে। বিভিন্ন ফুলের অগ্রভাগ তথা পুষ্পিকার মধ্যেও এধরনের গড়ন দেখা যায়; যেমন সূর্যমুখী ফুল কিংবা পাইন ফলের পাতা
সাধারণভাবে ব্যাপারটি জীববিজ্ঞানেরই কোনো একটি প্রক্রিয়া যা ডারউইনের বিবর্তন তত্বের সাথে সম্পর্কিত বলে কেউ ভাবতে পারেন। কিন্তু গবেষণায় দেখা গেছে, এটি আসলে সাধারণ পদার্থবিজ্ঞানের জ্ঞান-’সবচেয়ে কম বিভব শক্তিতে বিন্যস্ত হওয়ার মাধ্যমেই ঘটে। ১৯৯২ সালে বিজ্ঞানী Stephanie Douady এবং Yves Couder একটি পরীক্ষার মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেন। প্রথমে তারা চৌম্বকীয় তরলের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা (droplet of magnetic fluid) তেলের আবরণের ওপর ফেলেন। এরপর তেলের আবরণের সাথে উলম্বভাবে চৌম্বকক্ষেত্র প্রয়োগ করে ক্ষুদ্র চৌম্বকীয় কণাগুলোকে আহিত করেন। ফলস্বরূপ কণাগুলো সমধর্মে আহিত হবে এবং একে অপরকে বিকর্ষণ করবে। গবেষকরা এবার তেলের আবরণের পরিধি বরাবর আরেকটি চৌম্বকক্ষেত্র প্রয়োগ করে আহিত চৌম্বকীয় কণাগুলোকে কিনারা বরাবর টেনে আনা শুরু করলেন। দেখা গেল ক্ষুদ্র কণাগুলো ডাবল স্পাইরাল প্যাটার্নে বিন্যস্ত হয়েছে[৯৬]। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ডাবল, স্পাইরাল প্যাটার্ন জীবের অদ্বিতীয় কোনো বৈশিষ্ট্য নয়, এটি জীব, জড় সবার ধর্ম।
ছবি। পেজ ১২৭
চিত্র : সূর্যমুখী ফুলের ডাবল স্পাইরাল প্যাটার্ন
ছবি। পেজ ১২৮
চিত্র : ইলেক্ট্রনের ডাবল স্পাইরাল প্যাটার্ন
এছাড়া ব্যাপারটি ভিন্নভাবেও পরীক্ষা করে দেখেছেন অন্যান্য বিজ্ঞানীরা[৯৭]। তারা আহিত কণা (যেমন ইলেকট্রন) নিয়ে একই ধরণের পরীক্ষা করেছেন। বিভিন্ন কক্ষপথে সর্বনিম্ন বিভব শক্তির বিন্দুতে ইলেকট্রন স্থাপন করে তারা সেই একই প্যাটার্নের উদ্ভব লক্ষ্য করেছেন। হ্যাঁ! সেটি সেই ডাবল স্পাইরাল প্যাটার্ন। লক্ষ্য করুন এখানে নতুন কোনো অ্যালগোরিদম বা কোন বিশেষ নিয়ম কাজ করছে না, শুধু বিভব শক্তির সর্বনিম্ন ব্যবহার হচ্ছে।
শুধু প্রাকৃতিক নির্বাচন সকল কিছু ব্যাখ্যা করার জন্য হয়তো পর্যাপ্ত নয়। এর পাশাপাশি স্বতঃ সংগঠন ধর্মটি বিবর্তনের একটি বড় প্রভাবক বলে মনে করেন জীববিজ্ঞানী স্টুয়ার্ট কফম্যান[৯৮]। তিনি প্রস্তাব করেন, ক্যাটালাইটিক ক্লোসার (catalytic closure) নামক রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সেলফ সাসটেইনিং বিক্রিয়ার নেটওয়ার্ক উৎপন্ন হওয়ার মাধ্যমে প্রথম প্রাণের উৎপত্তি ঘটা সম্ভব। কফম্যান আরও বলেন, স্বতঃ সংগঠনকে নব্য আবিষ্কৃত প্রাকৃতিক নিয়ম মনে করা হলেও বাস্তবিক অর্থে এখানে মৌলিক পদার্থ বিজ্ঞান আর রসায়নের পরিচিত নিয়ম কানুন ছাড়া অন্য কোন নতুন ধারণা আরোপ করা হচ্ছে না। যাই হোক, জীবনের সূচনা কীভাবে হয়েছিল সেটি এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় নয়। প্রাণের উৎপত্তির একটি রূপরেখা নিয়ে আমরা কিছুটা আলোচনা করব এর পরে ‘ফ্রেডরিক হয়েলের বোয়িং ৭৪৭ ফ্যালাসি’ অধ্যায়ে। তবে, এমনটা ধরে ধরে নেওয়াটা অযৌক্তিক হবে না যে, জীবনের উৎপত্তিতে স্বতঃ সংগঠনের মতো রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের নীতির হাত ছিল। যদিও প্রাণের উৎপত্তি সংক্রান্ত একেবারে প্রান্তিক কিছু সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধান এখনও পাওয়া সম্ভব হয় নি, কিন্তু বিজ্ঞানীরা প্রতিদিনই নতুন নতুন জ্ঞানের আলোকে ধীরে ধীরে রহস্যের সর্বশেষ ধাপটিতে পৌঁছে যাচ্ছেন। আমরা মিডিয়ায় দেখেছি সম্প্রতি ক্রেগ ভেন্টর তার সিনথেটিক লাইফের গবেষণা থেকে প্রথম কৃত্রিম জীবকোষও তৈরি করতে সমর্থ হয়েছেন[৯৯]। কাজেই নিশ্চিত করেই বলা যায়, প্রাণের উৎপত্তি কিংবা মহাবিশ্বের উৎপত্তি কোনোকিছুর রহস্য সমাধানের ব্যাপারেই আমাদের ঈশ্বরের দ্বারস্থ হতে হবে না, বরং, কফম্যানের প্রস্তাব মতো, আধুনিক বিজ্ঞান থেকে পাওয়া বিভিন্ন অগ্রসর প্রস্তাব এবং অনুকল্পগুলো ঈশ্বরকে শূন্যস্থান থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে যথেষ্ট।
০৩. ফ্রেডরিক হয়েলের বোয়িং ৭৪৭ ফ্যালাসি
সরল, সাধারণ জ্ঞান দিয়ে বিচার করি বলে ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই। কোনো ঈশ্বরেই।
–চার্লি চ্যাপলিন
ছবি। পেজ ১৩০
চিত্র : ফ্রেডরিক হয়েল (১৯১৫-২০০১)
ফ্রেডরিক হয়েল (১৯১৫-২০০১) ছিলেন বিগত শতকের এক নামকরা জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী। আজকে যে আমরা মহাবিস্ফোরণ বা বিগব্যাং তত্বের কথা শুনি, সেই ‘বিগব্যাং’ শব্দটি তার কাছ থেকেই প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল ১৯৪৯ সালের একটা রেডিও প্রোগ্রামে, যদিও বিগব্যাং শব্দটি তিনি তখন উচ্চারণ করেছিলেন অনেকটাই সমালোচনা আর শ্লেষের সুরে। শ্লেষ থাকার কারণ, সেসময় বিগব্যাং-এর সাথে সমানে পাল্লা দিচ্ছিল। হয়েলেরই নিজস্ব একটি তত্ব; যাকে বিজ্ঞানীরা ডাকতেন স্থিতিশীল অবস্থা তত্ব (Steady State Theory) নামে। ১৯৬৪ সালে আর্নো পেনজ্যিাস এবং রবার্ট উইলসন মহাজাগতিক পশ্চাৎপট বিকিরণ[১০০] খুঁজে পাওয়ার আগ পর্যন্ত কিন্তু পৃথিবীর বহু নামকরা পদার্থবিজ্ঞানীই স্থিতিশীল অবস্থা তত্ত্বের প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। ফ্রেডরিক হয়েল ছিলেন সেই স্থিতিশীল তত্ত্বের মূল প্রবক্তা, যদিও তার এই বিখ্যাত তত্বের সাথে জড়িত ছিলেন আরও কয়েকজন নামকরা পদার্থবিদ-হারমান বন্দি, থমাস গোল্ড এবং পরবর্তীকালে এক ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী জয়ন্ত নারলিকর। স্থিতিশীল তত্ব ছাড়াও স্টেলার নিউক্লিওসিন্থেসিসসহ জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক কিছুতেই ফ্রেডরিক হয়েলের অবদান ছিল। জীবনের শেষ বয়সে তিনি তার ছেলের সাথে মিলে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি লেখায়ও হাত দিয়েছিলেন। বিজ্ঞানে তার সামগ্রিক অবদানের জন্য তিনি ‘স্যার’ উপাধি পেয়েছিলেন, পুরস্কার পেয়েছিলেন রয়েল এস্ট্রোনোমিকাল সোসাইটি থেকেও, এছাড়া আরও অন্যান্য ছোটখাটো পুরস্কার তো আছেই। কাজেই ফ্রেডরিক হয়েলের সুনাম কম ছিল না তার সময়ে।
ছবি। পেজ ১৩১
চিত্র : আর্কিওপটেরিক্স (১৪৭৭) : বার্লিন স্পেসিমেন
কিন্তু বড় বিজ্ঞানী হলে কী হবে তিনি বিভিন্ন জায়গায় নিজের মতামত দিতে পছন্দ করতেন। এমনি একটা ঘটনা ঘটেছিল যখন বিজ্ঞানীরা বিগত শতকের মাঝামাঝি সময়ে বেশ ক’টি ডায়নোসর এবং পাখির মধ্যবর্তী জীবাশ্ম আর্কিওপটেরিক্সের ফসিল খুঁজে পাচ্ছিলেন। হয়েল হঠাৎ করেই বলে বসলেন আর্কিওপটেরিক্সের ফসিলগুলো নাকি সব জালিয়াতি। অথচ, আর্কিওপটেরিক্স কিন্তু বিজ্ঞানীদের জন্য নতুন কিছু ছিল না সেসময়। আর্কিওপটেরিক্সের প্রথম পালকের ফসিল খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল বহু আগেই-সেই ১৮৬০ সালে। এমনকি ডারউইন তার অরিজিন অব স্পিশিজ গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণে আর্কিওপটেরিক্সের উল্লেখও করেছিলেন। ডারউইনের সমসাময়িক বিজ্ঞানী টিএইচ হাক্সলি তখনই মন্তব্য করেছিলেন যে, হাবভাবে মনে হচ্ছে আধুনিক পাখিগুলো সব থেরোপড ডাইনোসর থেকেই এসেছে; আর আর্কিওপটেরিক্সের মতো ফসিলগুলো এই যুক্তির পেছনে জোরালো প্রমাণ হিসেবে হাজির হয়েছে[১০১]। তারপর ১৮৬১ সালের দিকে জার্মানির ল্যাংগেনালথিমে[১০২] পাওয়া গেল আর্কিওপটেরিক্সের পূর্ণাঙ্গ কঙ্কাল। একই পরিক্রমায় ১৮৭৭ সালে ক্লমেনবার্গে[১০৩], ১৮৫৫ সালে রিডিনবার্গে, ১৯৫৪ সালে ল্যাংগেনালথিমে[১০৪], ১৯৫১ সালে ওয়ার্কারসজেলে, ১৯৬০ সালে জার্মানির ইৎসচাটে, ১৯৯১ সালে ল্যাংগেনালথিমে, ২০০৫ এবং ২০০৬ এ জার্মানিতে আর্কিওপটেরিক্সের বিভিন্ন ফসিল উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আর জীববিজ্ঞানীরা কষ্ট করে ফসিল পেলে কী হবে, বিজ্ঞানী হয়েল তার সহকর্মী গণিতবিদ চন্দ্র বিক্রমসিংহের সাথে মিলে হঠাৎ করেই ১৯৮৫ সালে তুমুল শোরগোল শুরু করলেন এই বলে যে, আর্কিওপটেরিক্সের ফসিলগুলো সব নাকি বানোয়াটা তাঁরা বললেন, ফসিলগুলো নাকি এত চমৎকারভাবে সংরক্ষিত থাকার কথা না, মধ্যবর্তী স্তরে নিশ্চয় আধুনিক পাখির পালক ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, ইত্যাদি। ব্রিটিশ ন্যাচারাল হিস্ট্রি জাদুঘরের বিজ্ঞানীরা হয়েলের প্রতিটি সন্দেহ
পরীক্ষা করে দেখলেন, এবং তাঁদের পরীক্ষায় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো ফসিলগুলো আর্কিওপটেরিক্সেরই। এমনি একটি পরীক্ষায় অ্যালেন চ্যারিগসহ অন্যান্য বিজ্ঞানীরা স্ল্যাবের কিনারাগুলোর মাপ নিয়ে দেখালেন আর্কিওপটেরিক্সের দুটি পাললিক শিলাস্তরের স্ল্যাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে একে অপরের স্তরে খাপ থেমে যায়, ফলে মধ্যবর্তী স্তরে আধুনিক পাখির পালক থাকার ব্যাপার এখানে নেই। তাদের সম্পূর্ণ পরীক্ষার ফলাফল সায়েন্স জার্নালের ১৯৪৬ সালের ২৩২ সংখ্যায় ‘আর্কিওপটেরিক্স কোনো জোচ্চুরি নয়’ শিরোনামে প্রকাশিত হ্যাঁ[১০৫] হয়েল যখন ফসিলের সত্যতা নিয়ে শোরগোল করছিলেন, ঠিক সেসময়ই জার্মানির সোলনহফেনে ১৯৮৭ সালে আরেকটি আর্কিওপটেরিক্সের ফসিল পাওয়া যায়, আর বিজ্ঞানীরা সবাই মিলে পুরো প্রক্রিয়াটিকে বস্তুনিষ্ঠ ভাবে অবলোকন করার সুযোগ পান। কীভাবে পাখির পালকের ছাপ পাললিক শিলায় পড়ে, কীভাবে শিলাস্তরে চিড় ধরে সবকিছুই বিজ্ঞানীরা আরও একবার ভালোমতো যাচাই করার সুযোগ পেযে যান। দেখা গেল আর্কিওপটেরিক্সের এই সোলনহফেন নমুনাটিও অন্যগুলোর মতোই একই ফলাফল নিয়ে আসলো। এই আবিষ্কারের ব্যাপারটিও সায়েন্স জার্নালে আর্কিওপটেরিক্সের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে আবির্ভূত হলো![১০৬] আর আর্কিওপটেরিক্স নিয়ে হয়েলের যাবতীয় ‘কন্সপিরেসি তত্বের সমাধি রচনা করল।
আসলে অধ্যাপক হয়েল পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে সুপরিচিত হলেও জীববিজ্ঞান কিংবা প্রত্নতত্ত্বের খুঁটিনাটি বিষয়ে সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন না; সত্যি বলতে কী বিবর্তন কিংবা পাললিক শিলায় কীভাবে ফসিল সংগৃহীত হয়, কীভাবে পালকের ছাপ স্ল্যাবে পড়ে এগুলো নিয়ে পরিষ্কার জ্ঞান হয়েলের ছিল না। কিন্তু সেই অপরিচ্ছন্ন জ্ঞান নিয়ে, তর্ক করে ভুল প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন পোড় খাওয়া জীববিজ্ঞানীদের কষ্টার্জিত সাক্ষ্য প্রমাণগুলোকে। অল্পবিদ্যা কীভাবে ভয়ংকর হয়ে ওঠে শেষপর্যন্ত নিজেকেই থেলো করে তোলে, হয়েলের দৃষ্টান্তই তার বড় প্রমাণ। এ প্রসঙ্গে টিম বেরা তার ইভল্যুশন অ্যান্ড দ্য মিথ অব ক্রিযেশনিজম : আ বেসিক গাইড টু দ্য ফেক্টস্ ইন দি ইভল্যুশন ডিবেট’ বইয়ে খুব স্পষ্টভাবেই বলেন[১০৭]:
একটি বিষয় পরিষ্কার করে বলা দরকার যে, হয়েল এবং বিক্রমসিংহ-এদের কারোই জীববিজ্ঞান এবং জীবাশ্মবিদ্যা বিষয়ে কোনো প্রথাগত জ্ঞান ছিল না, এবং তারা প্রাকৃতিক নির্বাচনের খুঁটিনাটি নিয়েও সম্যকভাবে অবগত ছিলেন না। ফলে তারা বিবর্তন-বিরোধী নানা চিন্তাভাবনা দিয়ে প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাদের এ সমস্ত অভিযোগ, তা যতই সারশূন্য আর মেধাশূন্য হোক না কেন, একটা সময় সৃষ্টিবাদীদের এক ধরনের স্বস্তি দিয়েছিল …। হয়েলের উদ্দেশ্য ঠিক স্পষ্ট ছিল না, কিন্তু তিনি একটি মুহূর্তের জন্যও নিজের বিশেষজ্ঞীয় ক্ষেত্রের মতো কোনো প্রভাবশালী চ্যালেঞ্জ এখানে আনতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এধরনের দাবি প্রমাণ করে, একজন। বিজ্ঞানী কেমন থেলো হয়ে যেতে পারেন যখন তিনি এমন বিষয়ে অভিমত জানাতে শুরু করেন যেখানে তিনি বিশেষজ্ঞ নন।
অধ্যাপক টিম বেরার কথায় অত্যুক্তি নেই। হয়েলের অভিযোগ কিংবা বিশ্লেষণগুলোতে কোনো সারবত্তা না থাকলেও সৃষ্টিবাদীদের জন্য সেগুলো তখন ভালোই রসদ যুগিযেছিল। ধর্মবাদী সাইটগুলো বুঝে না বুঝে হয়েলের ভুল অভিযোগগুলোই পুনরাবৃত্ত করে চললো (এবং কিছু ক্ষেত্রে এখনও চলছে)। তারা খোঁজ করে দেখারও চেষ্টা করেন নি যে, হয়েলের ভিত্তিহীন অভিযোগগুলো ন্যাচারাল হিস্ট্রি জাদুঘরের বিজ্ঞানীরা (যারা এ বিষয়ে সঠিক জ্ঞান রাখেন) ভুল প্রমাণ করে দিয়েছিলেন সেসময়ই।
হয়েল শুধু আর্কিওপটেরিক্স নিয়েই জল ঘোলা করেন নি, করেছিলেন আরও একটা বড় ব্যাপারে, যেটা নিয়ে সৃষ্টিবাদীরা এখনও যারপরনাই উচ্ছ্বসিত হয়েল তার ‘নিজস্ব গণনা থেকে একসময় সিদ্ধান্তে চলে এসেছিলেন যে, সরল অবস্থা থেকে উচ্চতর জটিল জীবের উদ্ভব অনেকটা নাকি টর্নেডোর ঝড়ে জাইয়ার্ডে পড়ে থাকা লোহার জঞ্জালের স্থূপ থেকে এক লহমায় বোয়িং ৭৪৭ বিমান তৈরি হয়ে যাওয়ার মতো অবাস্তব!
ছবি। পেজ ১৩৬
চিত্র : হয়েল ধারণা করেছিলেন যে, সরল অবস্থা থেকে উচ্চতর জটিল জীবের উদ্ভব অনেকটা নাকি টর্নেডোর ঝড়ে জাঙ্কইয়ার্ডের সৃপ থেকে বোয়িং ৭৪৭ বিমান তৈরি হয়ে যাওয়ার মতো অসম্ভাব্য কিছু!
মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, এই ‘জঞ্জাল থেকে বোয়িং ৭৪৭ বিমান তৈরি হওয়ার উপমা হয়েল কোনো বৈজ্ঞানিক সাময়িকীতে লেখেন নি। তবে শোনা যায় তিনি ১৯৮২ সালের একটি সেমিনারে প্রাণের রাসায়নিক উৎপত্তি তত্বের বিপরীতে তার প্যান্সপারমিয়া তত্ত্বের সপক্ষে একথা বলেছিলেন। ইস্টের সাথে বোয়িং ৭৪৭-এর তুলনা করার কারণ হিসেবে বলেছিলেন দুটোরই নাকি সমান সংখ্যক প্রত্যঙ্গ, এবং জটিলতার স্তরেও বেশ মিল আছে[১-৮]। যাহোক ফ্রেড হয়েলের এই যুক্তিমালা’ পরবর্তীকালে তার একটি বই ‘দ্য ইন্টেলিজেন্ট ইউনিভার্স’ (১৯৮৩)–এ সন্নিবেশিত হয়েছিল এভাবে[১০৯]–
ধরা যাক, একটি জাঙ্কইয়ার্ডে বোয়িং ৭৪৭ বিমানের সকল অংশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। হঠাৎ একটি ঘূর্ণিঝড় (whirlwind) এসে জাঙ্কইয়ার্ডের ওপর দিয়ে বয়ে চলে গেল। সেই ঘূর্ণিঝড়ে পুরো বোয়িং ৭৪৭ তৈরি হয়ে উড়ার জন্য প্রস্তুত অবস্থায় চলে আসার সম্ভাবনা বা চান্স কতটুকু?
তারপর থেকেই সৃষ্টিতাত্ত্বিকেরা সব জায়গায় হয়েলের উপমাকে বিবর্তনের বিরুদ্ধে এক মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার শুরু করেন।
শোনা যায় হয়েল ব্যক্তিগত জীবনে নাস্তিক হিসেবেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু সরল অবস্থা থেকে উচ্চতর জীবের উৎপত্তির সম্ভাবনা গণনা করতে গিয়ে দেখেন সেটার চান্স এতই কম (১০০০০০ ভাগের ১ ভাগ) যে, তাতে নাকি তার ‘নাস্তিকতার বিশ্বাস টলে গিযেছিল’ এবং হয়েল ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে পড়েন, এবং সেসময়ই তিনি ঘর্ণিঝডে বোয়িং ৭৪৭ তৈরি হওয়ার উপমা এনে দেখানোর চেষ্টা করেন যে, সরল অবস্থা থেকে জটিল জীবের উদ্ভব নাকি প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার, ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপ নাকি লাগবেই। এই গুজবের পেছনে আমরা কোনো সত্যতা খুঁজে না পেলেও (যদিও ব্যাপারটা সত্য হলেও খুব বেশি অবাক হব না) সম্প্রতি বইপত্র ঘাঁটার। ফলে একটা মজার জিনিস বেরিয়ে এসেছে। হলে কিন্তু কোনো সৃষ্টিবাদী বা ক্রিযেশনিস্ট ছিলেন না। বরং তার অনেক প্রবন্ধ এবং বইপত্রেই তিনি বিবর্তন তত্ত্বের ওপর প্রগাঢ় আস্থা ব্যক্ত করেছেন। যেমন, তার ‘অরিজিন অব লাইফ ইন দ্য ইউনিভার্স’ বইয়ে তিনি খুব স্পষ্ট করেই বলেন[১১০]–
We are inescapably the result of a long heritage of learning, adaptation, mutation and evolution, the product of a history which predates our birth as a biological species and stretches back over many thousand millennia…. Darwin’s theory, which is now accepted without dissent, is the cornerstone of modern biology. Our own links with the simplest forms of microbial life are well-nigh proven.
এমনকি তার জীবনের একেবারে শেষ দিককার বইগুলোতেও তিনি সৃষ্টিবাদকে প্রত্যাখ্যান করে লিখেছিলেন যে, কোনো প্রকৃত বিজ্ঞানী সৃষ্টিবাদে বিশ্বাস করতে পারেন না[১১১]। তারপরেও সৃষ্টিবাদীরা আর ধর্মবাদীরা হয়েলের বোয়িং ৭৪৭ উপমা নিয়ে যারপরনাই উচ্ছ্বসিত। এ যেন ঈশ্বরের অস্তিত্বের অকাট্য প্রমাণ তাদের কাছে। জাকির নায়েক, হারুন ইয়াহ্যিারা তো আছেই, আমরা শুনেছি সম্প্রতি বাংলাদেশের কিছু ধর্মীয় সংগঠন নাকি তাদের মুখপত্রে আর লিফলেটে ‘সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রমাণ হিসেবে হয়েলের যুক্তিমালা ব্যবহার করা শুরু করেছে। বোঝা যাচ্ছে কেবল কোরআন হাদিস। কিংবা অনুরূপ ধর্মগ্রন্থের আয়াতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা আর অপব্যাখ্যা হাজির করে আর কাজ চলছে না, তাদের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে বিবর্তন-বিশ্বাসী এবং সম্ভবত পাঁড় নাস্তিক হয়েলের উপমার কাছে। প্যালের ঘড়ির মৃত্যু নেই’ ঠিক তেমনই হয়ত বলা যেতে পারে ‘হয়েলের বোয়িং বিমানের মৃত্যু নেই! প্যালের ঘড়ি আর হয়েলের বোয়িং যেন পরস্পরের পরিপূরক; তামাক আর ফিল্টার দুজনে দুজনার!
এ অধ্যায়টি অবশ্য হয়েল আস্তিক নাকি নাস্তিক, সৃষ্টিবাদী না অসৃষ্টিবাদী তা নিয়ে বিতর্ক করার জন্য নয়, বরং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে তার আর্গুমেন্টগুলোকে যাচাই করে দেখা যে সত্যিই হয়েলের বোয়িং উপমা বিবর্তনের বিরুদ্ধে কোনো শক্তিশালী যুক্তি হিসেবে গ্রহণীয় হতে পারে কিনা। তবে তা যাচাই করার আগে একটি ব্যাপার পরিষ্কার বোধহয় করে নেওয়া দরকার যে, আধুনিক বিশ্বের প্রায় সকল জীববিজ্ঞানীরাই হয়েলের এই বোয়িং উপমাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন[১১২]। তারা মনে করেন হয়েলের এই বোয়িং ৭৪৭ উপমা বিবর্তনের সাথে তুলনীয় হতে পারে না। কারণ–
১. বিবর্তন টর্নেডো বা ঘূর্ণিঝড়ের মতো কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়। এটা এমন কোনো প্রক্রিয়া নয়, যেটাকে কেবল চান্স দিয়ে পরিমাপ এবং ব্যাখ্যা করতে হবে।
২. টর্নেডো দিয়ে চূড়ান্ত কোনোকিছু তৈরি করার চেষ্টা আসলে একধাপে ঘটা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় কোনোকিছু বানানোর চেষ্টা। আর অন্যদিকে বিবর্তন ঘটে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে বহু ধাপে পরিমিত ভিন্নতার মধ্য দিয়ে ক্রমবর্ধমান নির্বাচন (Cumulative Selection)-এর মাধ্যমে।
৩. প্রকৃতিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন সরঞ্জাম (যেমন জাঙ্কইয়ার্ডে রাখা বিমানের বিভিন্ন অংশ) জোড়া লাগার মাধ্যমে কিন্তু বিবর্তন ঘটে না। বিবর্তন ঘটে প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রভাবে শুধু বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যগুলো দীর্ঘ সময় ধরে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হওয়ার মাধ্যমে।
৪. বোয়িং বিমানের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত দ্রব্য থাকে স্থির। আর বোয়িং বিমান বানানোর পেছনে থাকে নকশাকারীর একটি চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য। অপরদিকে বিবর্তন কিন্তু কোনো ভবিষ্যতের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য মাথায় রেখে কাজ করে না, চূড়ান্ত লক্ষ্যের ব্যাপারে থাকে একেবারেই উদাসীন।
প্রথম দুটো পয়েন্ট আরেকটু বিস্তৃত করা যাক। অনেকেই ভেবে থাকেন প্রাথমিকভাবে মিউটেশনের ফলে বিভিন্ন প্রকরণের অভদ্য যেহেতু ইতস্তত : বিক্ষিপ্তভাবে (randomly) ঘটে থাকে, বিবর্তন বোধহয় কেবল চান্সের থেলা। আসলে কিন্তু তা নয় মোটেই। বিবর্তনের পেছনে মূল চালিকা শক্তি হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচন। প্রাকৃতিক নির্বাচন ব্যাপারটা কিন্তু কোনো চান্স নয়। প্রাথমিক পরিব্যক্তিগুলো র্যান্ডম হতে পারে, কিন্তু তারপর বৈশিষ্ট্যগুলো ন্যাচারাল সিলেকশনের মাধ্যমে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটি ‘র্যান্ডম’ নয়, বরং ‘ডিটারমিনিস্টিক’, কারণ তা নির্ভর করে বিদ্যমান উপযুক্ত পরিবেশ এবং সে পরিবেশে অনুকূল কোন বৈশিষ্ট্যের টিকে থাকার ওপর। সেজন্যই বিবর্তন কেবল চান্সের খেলা নয়।[১১৩] পরিব্যক্তিগুলো র্যান্ডম হওয়ার পরেও কীভাবে তা বিবর্তনকে একটি নির্দিষ্ট দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে, তা জানতে ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘If Mutation is Random, Why Does Evolution Occur at all? প্রবন্ধটি পড়া যেতে পারে। প্রবন্ধটিতে দুটি চমৎকার উদাহরণ হাজির করে বুঝানো হয়েছে- Mutation was random, but selection provided a direction to the evolution.’
ছবি। পেজ ১৪১
চিত্র : চোখের বিবর্তন : চোখের মতো একটি জটিল প্রত্যঙ্গ সহজেই আলোর প্রতি সংবেদনশীল খুব সরল স্নায়বিক কোষ বিশিষ্ট ‘আই-স্পট’ থেকে বিভিন্ন ধাপে ধাপে পরিমিত ভিন্নতার মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হতে পারে। যখনই এধরনের কোনো পরিবর্তন-যা কিছুটা হলেও বাড়তি সুবিধা প্রদান করে, তা ধীরে ধীরে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে জনপুঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে।
এ প্রসঙ্গে আমাদের চোখের অভ্যুদয় এবং বিকাশের ব্যাপারটা আরও বিস্তৃতভাবে চিন্তা করা যেতে পারে। আজকে আমরা চোখের যে পূর্ণাঙ্গ গঠন দেখে বিস্মিত হই, তা কিন্তু একদিনে তৈরি হয় নি, বরং বহুকাল ধরে ক্রমান্বয়ে ঘটতে থাকা ছোট ছোট পরিবর্তনের ফল হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে। খুব সম্ভবত আলোর প্রতি সংবেদনশীল এক ধরনের স্নায়বিক কোষ থেকে প্রথম চোখের বিকাশ শুরু হয়। তারপর হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্নভাবে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হতে হতে আজকে তারা এই রূপ গ্রহণ করেছে। কতগুলো সংবেদনশীল কোষকে কাপের মতো অবতলে যদি ঠিকমতো সাজানো যায় তাহলে যে নতুন একটি আদি চোখের উদ্ভব হয় তার পক্ষে আলোর দিক নির্ণয় করা সম্ভব হয়ে ওঠে। এখন যদি কাপটির ধারগুলো কোনোভাবে বন্ধ করা যায়, তাহলে আধুনিক পিন হোল ক্যামেরার মতো চোখের উৎপত্তি ঘটবে।
তারপরে এক সময় গতি নির্ধারণ করতে পারে এমন একটি অক্ষিপট বা রং বুঝতে পারে এমন কোণের মতো অংশ বিকাশ লাভ করে, তাহলে উন্নত একটি চোখের উৎপত্তি হবে। এরপর যদি বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আইরিস ডায়াফ্রামের উৎপত্তি ঘটে তাহলে চোখের ভেতরে কতখানি আলো ঢুকবে তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। হবে। এরপর আস্তে আস্তে যদি লেন্সের উদ্ভব ঘটে তা তাকে আলোর সমন্বয় এবং ফোকাস করতে সহায়তা করবে, আর এর ফলে চোখের উপযোগিতা আরও বাড়বে।
ছবি। পেজ ১৪২
চিত্র : প্রকৃতিতে পাওয়া বিভিন্ন ধরনের চোখ খুব সরল ধরনের চোখ থেকে শুরু করে জটিল চোখের অস্তিত্ব এই প্রকৃতিতেই আছে, আর তা সবই তৈরি হয়েছে বিবর্তনের ধারাবাহিকতায়[১১৪]
এভাবেই সময়ের সাথে সাথে প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রভাবে উপযোগিতা নির্ধারণ করে চোখের ক্রমান্বযিক পরিবর্তন ঘটেছে। আমরা এখনও আমাদের চারপাশে বিবর্তন প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত বিভিন্ন ধাপের চোখের অস্তিত্ব দেখতে পাই, অনেক আদিম প্রাণীর মধ্যে এখনও বিভিন্ন রকমের এবং স্তরের আদি-চোখের অস্তিত্ব দেখা যায়।
কিছু এককোষী জীবে একটা আলোক-সংবেদনশীল জায়গা আছে যা দিয়ে সে আলোর দিক সম্পর্কে খুব সামান্যই ধারণা করতে পারে, আবার কিছু কৃমির মধ্যে এই আলোক-সংবেদনশীল কোষগুলো একটি ছোট অবতল কাপের মধ্যে বসানো থাকে যা দিয়ে সে আরেকটু ভালোভাবে দিক নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। সমতলের উপর বসানো নামমাত্র আলোক সংবেদনশীলতা থেকে শুরু করে পিনহোল ক্যামেরা সদৃশ চোখ কিংবা মেরুদণ্ডী প্রাণীদের অত্যন্ত উন্নত চোখ পর্যন্ত সব ধাপের চোখই দেখা যায় আমাদের চারপাশে (অন্ধ গুহা মাছ মেক্সিকান টেট্রা থেকে শুরু করে নটিলাস, প্লানারিয়াম, অ্যান্টার্কটিক ক্রিল, মৌমাছি, মানুষের চোখ ইত্যাদি), এবং তা দিয়েই বিবর্তন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর ব্যাখ্যা করা সম্ভব। বিবর্তন প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে ক্রমবর্ধমান নির্বাচনের মাধ্যমে না ঘটলে আমরা প্রকৃতিতে এত বিভিন্ন ধরনের চোখের অস্তিত্ব পেতাম না। সম্প্রতি সুইডিশ অধ্যাপক ড্যান এরিক নিলসন এবং পেলগার তাঁদের গবেষণার মাধ্যমে[১১৫] বের করে দেখিয়েছেন যে, আদি সমতল পিগমেন্টেড আলোক সংবেদনশীল সেল থেকে শুরু করে প্রায় ২০০০ ধাপের মধ্যে পরে তা মানুষের চোখের মতো জটিল যন্ত্রে পরিবর্তিত হতে পারে। তাদের করা সিমুলেশনের সচিত্র ফলাফল নিচে দেওয়া হলো–
ছবি। পেজ ১৪৪
চিত্র : অধ্যাপক ড্যান এরিক নিলসন এবং পেলগারের সিমুলেশনের ফলাফল, তারা দেখিয়েছেন আদি সমতল আলোক সংবেদনশীল সেল থেকে শুরু করে ৪০০ ধাপ পরে তা রেটিনাল পিটের আকার ধারণ করে, ১০০০ ধাপ পরে তা আকার নেয় পিনহোল ক্যামেরার মতো আকৃতির, আর প্রায় ২০০০ ধাপ পরে অক্টোপাসের মতো জটিল চোখের উদ্ভব ঘটে। জীববিজ্ঞানী মার্ক রিডলির সাইটে ব্যাপারটি এনিমেশনের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।
এবার হয়েলের সম্ভাবনার মারপ্যাঁচ নিয়ে একটু গভীরে আলোচনা যাক হয়েলের এই জঞ্জাল থেকে বোয়িং উপমা খুব মৌলিক কিছু নয়। অসীম বানর তত্ব (Infinite monkey theorem) নামে একটি ব্যাপার দর্শনের আঙ্গিনায় প্রচলিত ছিলই। হলে সেটাকে বোয়িং এর আলোকে কোষীয় প্রাণবিজ্ঞানের আঙ্গিনায় ব্যবহার করতে চেযেছেন। মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে নামের বইয়ে এই অসীম বানর তত্ব নিয়ে ছোট করে লিখা হয়েছিলো[১১৬]। পাঠকের সামনে সেটি একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন বোধ করছি।
অসীম বানর তত্ব হচ্ছে এমন একটা ধারণা যেখানে মনে করা হয় যে, অফুরন্ত সময় দেওয়া হলে আপাত দৃষ্টিতে প্রায় অসম্ভব সমস্ত ব্যাপারও ঘটে যেতে পারে সম্ভাবনার নিয়মেই। যেমন, একটা বানরকে যদি টাইপরাইটারের সামনে বসিয়ে দেওয়া হয়, তবে তার অন্ধভাবে টাইপিং করা থেকে শেক্সপিয়ারের হ্যামলেটও বেরিয়ে আসতে পারে, যদি বানরটিকে অফুরন্ত সময় দেওয়া হয় টাইপিং চালিয়ে যাওয়ার জন্য। হয়েল এই বানরের বিক্ষিপ্তভাবে টাইপ করে হ্যামলেট লেখার উপমাকেই প্রাকৃতিক উপায়ে জটিল জীবজগৎ তৈরির ব্যাখ্যায় নিয়ে গেছেন, কেবল পার্থক্য এই যে, তিনি শেক্সপিয়ারের হ্যামলেটের বদলে ব্যবহার করেছেন বোয়িং ৭৪৭।
হয়েলের ধারণা সত্য হলে সরল অবস্থায় প্রাকৃতিকভাবে জটিল জীবজগতের উদ্ভব অনেকটা হঠাৎ লটারি জিতে কোটিপতি হওয়ার মতোই একটা ব্যাপার হবে। কম সম্ভাবনার ঘটনা যে ঘটে না তা নয়। অহরহই তো ঘটছে। ভূমিকম্পে বাড়ি-ঘর ধ্বসে পড়ার পরও অনেক সময়ই দেখা গেছে ঘটনাক্রমে ভগ্নস্তূপের নিচে কেউ বেঁচে আছেন। এই যে হাইতিতে বিশাল ভূমিকম্প হলো কিছুদিন আগে, প্রায় পনেরো দিন, এমনকি একটি ক্ষেত্রে ২৭ দিন পরেও জীবন্ত অবস্থায় এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করা হয়েছে[১১৭]। বাংলাদেশে ২০১৩ সালে রানা প্লাজা ভবন ধ্বসের ১৭ দিন পর ধ্বংসস্তূপের নিচ থেকে রেশমাকে জীবিত উদ্ধারের ঘটনা বিশ্বজুড়ে বিস্ময় ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল (যদিও ঘটনাটি সাজানো নাটক’ কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে)। নিউইয়র্ক টাইমস-এ একবার এক মহিলাকে নিয়ে প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল যিনি দু দুবার নিউজার্সি লটারির টিকেট জিতেছিলেন। তারা সম্ভাবনা হিসাব করে দেখেছিলেন ১৭ ট্রিলিয়নে ১L এত কম সম্ভাবনার ব্যাপারও ঘটছে। কাজেই সম্ভাবনার নিরিখেই প্রাণের উৎপত্তি এবং সর্বোপরি জটিল জীবজগতের উদ্ভব যত কম সম্ভাবনার ঘটনাই হোক না কেন, ঘটতে পারে। সম্ভাবনা নিয়ে যে অনেক ধরনের চালাকি করা সম্ভব সেটা পাঠকরা আগের অধ্যায়ের অসম্ভাব্যতা অংশে দেখেছেন।
প্রাণের আবির্ভাব ও বিবর্তনের পেছনে জীববিজ্ঞানীদের কাছে কেবল সম্ভাবনার মারপ্যাঁচ থেকেও ভালো উত্তর রয়েছে। আর সেই উত্তরটি হচ্ছে প্রাকৃতিক নির্বাচন আর পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, প্রাকৃতিক নির্বাচন কোনো চান্সের খেলা নয়। এটি একটি নন র্যান্ডম ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়া। সেজন্যই ব্লাইন্ড ওযাচমেকার গ্রন্থে অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স পরিষ্কারভাবেই বলেছেন[১১৮]–
প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটা ডারউইনীয় বিবর্তনকে এলোমেলো (random) মনে করা শুধু ভুলই নয়, চূড়ান্ত বিচারে অসত্য। এটা সত্যের পুরোপুরি বিপরীত। চান্স’ ডারউইনীয় রেসিপিতে খুব ছোট একটা উপাদান, কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ বড় উপাদানটির নাম ক্রমবর্ধমান নির্বাচন যেটা একেবারেই নন-র্যান্ডম।
এ প্রসঙ্গে একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আমাদের গ্যালাক্সিতে ১০১১ টি তারা আর ১০৬০ টি ইলেকট্রন আছে। ঘটনাক্রমে এ ইলেকট্রনগুলো একত্রিত হয়ে আমাদের গ্যালাক্সি, কোটি কোটি তারা, আমাদের পৃথিবী এবং শেষ পর্যন্ত এই একটি মাত্র গ্রহে উপযুক্ত পরিবেশে প্রথম জীবকোষটি গঠনের সম্ভাবনা কত? আমাদের গ্যালাক্সি এবং পৃথিবীর যে ব্যস, তা কি ওই সম্ভাবনা সফল করার জন্য যথেষ্ট? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব কঠিন। কারণ এই সম্ভাবনা মাপতে গেলে যে হাজারটা চলক নিয়ে কাজ করতে হয়, তার অনেকগুলো সম্বন্ধে। আমরা এখনও অনেক কিছু ঠিকমতো জানি না। তারপরেও এটা নিদ্বিধায় বলা যায় যে, হয়েলের মতো শুধু চান্স দিয়ে পরিমাপ করে একধাপী সমাধান হাজির করলে সেটার সম্ভাবনা এতই কম বেরুবে যে ‘জঞ্জাল থেকে বোয়িং হওয়ার মতোই শোনাবে; কিন্তু প্রাকৃতিক নির্বাচনকে গোনায় ধরলে আর সেটা মনে হবে না। বিজ্ঞানী কেযুরেন্স-স্মিথ এমনই একটি কৃত্রিম উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি আমাদের বুঝিয়েছিলেন ১৯৭০ সালেই। তিনি বলেছেন, ধরা যাক একটা বানরকে জঙ্গল থেকে ধরে নিয়ে এসে টাইপরাইটারের সামনে বসিয়ে দেওয়া হলো। তারপর তার সামনে ডারউইনের ‘প্রজাতির উৎপত্তি’ নামক বইটি খুলে এর প্রথম বাক্যটি টাইপ করতে দেওয়া হলো। বাক্যটি এরকম
When on board HMS Beagle, as a naturalist, I was much struck with certain facts in the distribution of the inhabitants of South America, and in the geological relations of the present to the past inhabitants of that continent.
এই লাইনটিতে ১৮২টি অক্ষর আছে। বানরটিকে বলা হলো এই লাইনটিকে সঠিকভাবে কাগজে ফুটিয়ে তুলতে। এখন বানর যেহেতু অষ্কর চিনে না, সেহেতু সে টাইপরাইটারের চাবি অন্ধভাবে টিপে যাবে। টিপতে টিপতে ঘটনাক্রমে একটি শব্দ সঠিকভাবে টাইপ হতেও পারে। কিন্তু শুধু সবগুলো শব্দ সঠিকভাবে টাইপ নয়, এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। এখন এই বানরটির বাক্যটি সঠিকভাবে টাইপ করার সম্ভাবনা কত? কত বছরের মধ্যে অন্তত একবার হলেও বানরটি সঠিকভাবে বাক্যটি টাইপ করতে পারবে? সম্ভাবনার নিরিখে একটু বিচার-বিশ্লেষণ করা যাক।
ছবি। পেজ ১৪৮
চিত্র : অনেকে ভাবেন, একটা বানরকে যদি টাইপরাইটারের সামনে বসিয়ে দেওয়া হয়, তবে তার অন্ধভাবে টাইপিং করা থেকে শেক্সপিপিয়রের হ্যামলেট বেরিয়ে আসলে আসতেও পারে, যদি বানরটিকে অফুরন্ত সময় দেওয়া হয় টাইপিং চালিয়ে যাওয়ার জন্য।
মনে করা যাক যে, টাইপরাইটারটিতে ৩০টি অক্ষর আছে এবং বানরটি প্রতি মিনিটে ৬০টি অক্ষর টাইপ করতে পারে। শব্দের মধ্যে ফাঁক-ফোকরগুলো আর বড় হাত ছোট হাতের অক্ষরের পার্থক্য এই গণনায় না আনলেও, দেখা গেছে পুরো বাক্যটি সঠিকভাবে টাইপ করতে সময় লাগবে ১০৮০ বছর, মানে প্রায় অনন্তকাল! কিন্তু যদি এমন হয় যে, একটি সঠিক শব্দ লেখা হওয়ার সাথে সাথে সেটিকে আলাদা করে রাখা হয়, আর বাকি অক্ষরগুলো থেকে আবার নির্বাচন করা হয় বানরের সেই অন্ধ টাইপিং-এর মাধ্যমে, তবে কিন্তু সময় অনেক কম লাকবে, তারপরও ১৭০ বছরের কম নয়। কিন্তু যদি এই নির্বাচন শব্দের উপর না হয়ে অক্ষরের ওপর হয়ে থাকে (অর্থাৎ, সঠিক অক্ষরটি টাইপ হওয়ার সাথে সাথে এটিকে আলাদা করে রেখে দেওয়া হয়); তবে কিন্তু সময় লাগবে মাত্র ১ ঘণ্টা, ৩৩ মিনিট, ৩০ সেকেন্ড।
কাজেই উপরের উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, প্রাকৃতিক নির্বাচনকে গোনায় ধরলে ব্যাপারগুলো আর ‘অসম্ভব’ থাকে না, বরং অনেক সহজ হয়ে যায়। নিঃসন্দেহে পরীক্ষাটি গুরুত্বপূর্ণ তারপরেও ওপরের উদাহরণটির কিছু ত্রুটি আছে। একে তো এধরনের প্রোগ্রাম খুব সরল, তার উপর সঠিক বাক্য বা অক্ষর নির্বাচিত হওয়ার সাথে সাথে সেটিকে আলাদা করে রাখার ব্যাপারটা কিন্তু সেইভাবে প্রাকৃতিক নির্বাচনকে প্রকাশ করে না। প্রাকৃতিক নির্বাচন জিনিসটি তাহলে কী? আগের অধ্যায়ে আমরা প্রাকৃতিক নির্বাচন জিনিসটার একটা বিস্তৃত ব্যাখ্যা পেয়েছি। বেছে নিয়েছিলাম নিচের তিনটা ধাপকে[১১৯]–
১. জনপুঞ্জের অধিবাসীরা নিজেদের প্রতিলিপি তৈরি করে (জীববিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন রেপ্লিকেশন)।
২. প্রতিলিপি করতে গিয়ে দেখা যায় প্রতিলিপিগুলো নিখুঁত হয় না, অনেক ভুলত্রুটি ভাল হয়ে যায় (জীববিজ্ঞানীরা একে বলেন ‘মিউটেশন বা পরিব্যক্তি)।
৩. এই ভুল কারণে প্রজন্মে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের তারতম্য ঘটে (জীববিজ্ঞানীরা বলেন ‘ভ্যারিয়েশন’ বা প্রকরণ)।
কাজেই প্রতিলিপি, পরিব্যক্তি এবং প্রকরণের সমন্বয়ে যে নির্বাচন প্রক্রিয়া জীবজগতের জনপুঞ্জে যে পরিবর্তনের জন্য দায়ী তাকেই আমরা প্রাকৃতিক নির্বাচন নামে অভিহিত করব। এই ধরনের প্রাকৃতিক নির্বাচনকে গোনা ধরলে আমাদের উপরের সমস্যাটা কীভাবে সমাধান করতে হবে? করতে হবে মিউটেশন এবং রেপ্লিকেশনের ব্যাপারটা মাথায় রেখে এবং সেখান থেকে শুরু করে।
বিক্ষিপ্ত পরিব্যক্তি (random mutation) এবং প্রতিলিপির (replication) ব্যাপারটা মাথায় রেখে অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স নিজ হাতে আশির দশকে একটি প্রোগ্রাম লেখেন, প্রথমে জি ডালিউ বেসিক ভাষায়, এবং পরে প্যাস্কেলে, যেটাকে এখন অভিহিত করা হয় Weasel Program নামে, সেটি পরে তিনি প্রকাশ করেন তার বিখ্যাত ব্লাইন্ড ওযাচমেকার’ বইয়ে। বানর দিয়ে পুরো হ্যামলেট না লিখে তিনি হ্যামলেট এবং পলোনিয়াসের মধ্যকার কথোপকথনের একটি উদ্ধৃতি METHINKS IT IS LIKE A WEASEL সিমুলেশনের জন্য তার প্রোগ্রামে ব্যবহার করেন। তবে তিনি অন্ধভাবে টাইপরাইটার বা কিবোর্ড চালনাকারী কোনো বানর খুঁজে পান নি, তার বদলে তিনি ব্যবহার করেছিলেন তার এগারো মাস বয়সী কন্যাকে কম্পিউটারের কিবোর্ডের সামনে বসিয়ে দিয়ে। তার কন্যা কম্পিউটারের কিবোর্ডে হাত রেখে টাইপ করেছিল নিচের অর্থহীন কিছু অক্ষরমালা–
WDLTMNLT DTJBKWIRZREZLMQCO P
এই অক্ষরমালাকেই তিনি প্রতি জেনারেশন বা প্রজন্মে প্রতিলিপি করতে দেন ডকিন্স। যেহেতু তিনি জানতেন জীবজগতে প্রতিলিপিগুলো নিখুঁত হয় না, অনেক ভুল হয়ে যায় (অর্থাৎ মিউটেশন ঘটে), ডকিন্সও প্রতিলিপিতে কিছু ভুল হওয়ার সুযোগ করে দেন তার সিমুলেশনে, ফলে প্রতি প্রজন্মে একটি বা দুটি অক্ষর পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ার সুযোগ থাকতো। তিনি এভাবে সিমুলেশন করে এগিয়ে গিয়ে অনেকটা এধরনের ফলাফল পেলেন
প্রজন্ম ০১: WDLTMNLT DTJBKWIRZREZLMQCO P
…
প্রজন্ম ০২ : WDLTMNLT DTJBSWIRZREZLMQCO P
…
প্রজন্ম ১০: MDLDMNLS ITJISWHRZREZ MECS P
…
প্রজন্ম ২০ : MELDINLS IT ISWPRKE Z WECSEL
…
প্রজন্ম ৩০: METHINGS IT ISWLIKE B WECSEL
…
প্রজন্ম ৪০ : METHINKS IT IS LIKE I WEASEL
…
প্রজন্ম ৪৩ : METHINKS IT IS LIKE A WEASEL
অর্থাৎ একেবারেই অর্থহীন কিছু অক্ষরমালা থেকে ৪৩ প্রজন্ম পরে তিনি METHINKS IT IS LIKE A WEASEL-এর মতো অর্থপূর্ণ বাক্যাংশ গঠিত হতে দেখলেন। ডকিন্স তার ব্লাইন্ড ওয়াচমেকার বইয়ে বলেছেন, তিনি যখন প্রথমে বেসিক ভাষায় প্রোগ্রামটি লিখে লাঞ্চের জন্য আধা ঘন্টা বাইরে গিয়েছিলেন, ফিরে এসে দেখেন এর মধ্যেই METHINKS IT IS LIKE A WEASEL বেরিয়ে গিয়েছিল। পরে তিনি একই প্রোগ্রাম, প্যাস্কাল ব্যবহার করে লিখেছিলেন এবং তাতে সময় লেগেছিল মাত্র ১১ সেকেন্ড ইন্টারনেটে ইউটিউবে ডকিন্সের সিমুলেশন সংক্রান্ত কিছু ভিডিও রাখা আছে।[১২০] সেগুলো থেকে ডকিন্সের সিমুলেশন সম্বন্ধে পাঠকেরা কিছুটা ধারণা পেতে পারেন। এছাড়া, ১৯৮৪ সালের দিকে গ্লেনডেল কলেজের রিচার্ড হার্ডিসন একই ধরনের স্বতন্ত্র একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরি করে তাতে দেখান যে এভাবে র্যান্ডম মিউটেশন বা পরিব্যক্তি ঘটতে দিয়ে’ শেক্সপিয়ারের গোটা হ্যামলেট নাটিকাটি সাড়ে চার দিনে একেবারে অগোছালো অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ সঠিকভাবে পুনর্বিন্যস্ত করা সম্ভব।[১২১]
তারপরেও ডকিন্সের সিমুলেশনেরও কিছু সমালোচনা আছে। তার প্রোগ্রামও সরলতার দোষে দুষ্ট। এছাড়া তার প্রোগ্রাম একটি সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যকে (longterm goal) সামনে রেখে চালিত (এ ক্ষেত্রে অভীষ্ট লক্ষ্যটি ডকিন্সই নির্বাচন করেছিলেন-METHINKS IT IS LIKE A WEASEL)। বিবর্তন কিন্তু এধরনের কোনো সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগোয় না। তিনি নিজেই ‘ব্লাইন্ড ওযাচমেকার’ বইয়ে তার প্রোগ্রামের এই সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছিলেন এভাবে
Although the monkey/Shakespeare model is useful for explaining the distinction between single-step selection and cumulative selection, it is misleading in important ways. One of these is that, in each generation of selective ‘breeding’, the mutant ‘progeny’ phrases were judged according to the criterion of resemblance to a distant ideal target, the phrase METHINKS IT IS LIKE A WEASEL. Life isn’t like that. Evolution has no long-term goal. There is no long-distance target, no final perfection to serve as a criterion for selection, although human vanity cherishes the absurd notion that our species is the final goal of evolution. In real life, the criterion for selection is always short-term, either simple survival or, more generally, reproductive success.
অবশ্য ডকিন্সের এই উইসেল প্রোগ্রাম এই অর্থেই গুরুত্বপূর্ণ যে, তিনি দেখালেন পরিব্যক্তি এবং প্রতিলিপির প্রভাবে ঘটা ক্রমবর্ধমান নির্বাচনের মাধ্যমে আপাত অসম্ভব বলে মনে হওয়া ঘটনাও স্বাভাবিক নিয়মে ঘটতে পারে। সেজন্যই তিনি তার বইয়ে বলেন
ক্রমবর্ধমান নির্বাচন জীবনের অস্তিত্বের সমস্ত আধুনিক ব্যাখ্যার চাবিকাঠি। এটা এক বিনি সূতার মালা গ্রন্থিত করে চলে খুব সৌভাগ্য প্রসূত ঘটনা (বিক্ষিপ্ত পরিব্যক্তি) গুলোকে অবিক্ষিপ্ত এক অনুক্রমে; ফলে অনুক্রমের শেষে এসে আমরা যখন চূডান্ত কাঠামোর দিকে তাকাই তখন আমাদের মধ্যে এক ধরনের বিভ্রম তৈরি হয়; আমরা ভাবি এধরনের কাঠামো তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা এতই কম যে, চান্সের মাধ্যমে এমনই একটি কাঠামো তৈরিতে যে সময় লাগবে-তার তুলনায় সমগ্র মহাবিশ্বের ব্যসও খুব নগণ্য।
ডকিন্স পরে তার প্রোগ্রামটিকে আরও উন্নত করেন, এবং METHINKS IT IS LIKE A WEASEL বাদ দিয়ে কোনো সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য ছাড়াই সিমুলেশন ঘটান। গাছের থেকে যেমন শাখা-প্রশাখা বিস্তার লাভ করে, ঠিক সেভাবেই ‘জিন নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তনকে কম্পিউটারে চালিত করে সরল অবস্থা থেকে মাকড়সা কিংবা অক্টোপাস সদৃশ জটিল জীবজগতের কাঠামো তৈরি করে দেখান, তার সেই প্রোগ্রামের নাম দেন ‘বায়োমর্ফ’[১২২]।
ডকিন্স তার পরবর্তী বই ‘ক্লাইম্বিং মাউন্টেন্ট ইম্প্রোবেবল’-এ অন্য প্রোগ্রামারদের লেখা আরও কিছু জটিল প্রোগ্রামের উল্লেখ করেন বিবর্তনের বাস্তবসম্মত মডেল তুলে ধরতে। এ ধরনের বহু মডেল ইন্টারনেটের বিজ্ঞানের ওপর গবেষণালব্ধ বিভিন্ন ওয়েবসাইটেও পাওয়া যাবে।[১২৩] সম্প্রতি স্কেপ্টিকাল এনকুইরার পত্রিকায় গবেষক ডেভ থমাস তার ‘War of Weasels : An Evolutionary Algorithm Beats Intelligent Design’ প্রবন্ধে একটি আকর্ষণীয় বিষয়ের অবতারণা করেন।[১২৪] তিনি দেখিয়েছেন যে, ইন্টারনেটে কম্পিউটার প্রোগ্রামের একটি প্রতিযোগিতা হয়েছিল যেখানে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের অ্যালগোরিদমের সাথে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল বিবর্তনীয় অ্যালগোরিদমের ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের সমর্থক সালভেদর কর্ডোভাসহ অনেকেই বিবর্তনকে পরাজিত করতে তাদের শক্তিশালী অ্যালগোরিদম হাজির করেছিলেন। কিন্তু তারপরেও তাদের বিবর্তনীয় জেনেটিক অ্যালগোরিদমের কাছে শোচনীয় পরাজয় ঘটে। ডেভ থমাস তার প্রবন্ধে তাই পরিষ্কার করেই বলেন–
The results were stunning: The official representative of intelligent design community was outperformed by evolutionary algorithm, thus learning Orgel’s Second Law-’Evolution is smarter than you are’-the hard way.
এ গাণিতিক সিমুলেশনের সবগুলোই আমাদের খুব পরিষ্কারভাবে দেখিয়েছে যে নন-র্যান্ডম প্রাকৃতিক নির্বাচনের প্রভাবে জটিল জীবজগতের উদ্ভব ঘটতে পারে, কোনো ধরনের কল্পিত শক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়াই। মূলত অধ্যাপক হয়েল প্রাকৃতিক নির্বাচন ব্যাপারটা ঠিকমতো বোঝেননি বলেই তিনি জটিল জীবজগতের উদ্ভবকে কেবল চান্স দিয়ে পরিমাপ করতে চেযেছিলেন এবং একে বোয়িং ৭৪৭ উপমার সাথে তুলনা করে ফেলেছিলেন। এমনকি হয়েলের চান্সের গণনাও সম্প্রতি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। যেমন, টক অরিজিন সাইটে ড. ইয়ান appare Lies, Damned Lies, Statistics, and Probability of Abiogenesis Calculations প্রবন্ধে[১২৫] হয়েলের অজৈবজনি। (Abiogenesis) সংক্রান্ত গণনার নানা ভুলভ্রান্তির প্রতি নির্দেশ করেছেন। একটি ভ্রান্তি এই যে, হয়েল সম্ভাবনা পরিমাপের সময় প্রতিটি ঘটনাকে একটির পরে একটি এভাবে সিরিজ বা অনুক্রম আকারে সাজিয়েছিলেন। কিন্তু প্রকৃতির সিমুলেশনগুলো এভাবে সিরিজ আকারে ঘটে নি, অনেকগুলোই ঘটেছে সমান্তরালভাবে। ফলে সময় লেগেছে অনেক কম। আপনার চার জন বন্ধুকে চারটি মুদ্রা হাতে ধরিয়ে দিয়ে ঝোঁকমুক্তভাবে নিক্ষেপের সুযোগ করে দিলে-চারটি HHHH পেতে যে সময় লাগবে, সেই একই কাজ পেতে আপনার ষোল জন বন্ধুকে লাগিয়ে দিলে অনেক তাড়াতাডিই কাঙ্ক্ষিত ফলাফল (অর্থাৎ চারটি HHHH) বেরিয়ে আসবে। ঠিক একইভাবে, একটি বানর দিয়ে পুরো হ্যামলেট পাওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম মনে হলেও, যদি এক লক্ষ বানরকে একই কাজে লাগিয়ে দেওয়া যায়, তবে আর সেরকম অসম্ভব কিছু মনে হবে না। ইয়ান মাসগ্রেভ তার প্রবন্ধে যথার্থই বলেছেন, যদি এক বিলিয়ন ভাগের এক ভাগ সম্ভাবনার কোনো কিছু। ঘটিযে দেখাতে চান তা হলে চীনের জনসংখ্যার মতো চলক নিযুক্ত করে দিন। আর ডকিন্সের মতো ইয়ান মাসগ্রেভও মনে করেন, সৃষ্টিবাদীদের বোয়িং উপমার সাথে বিবর্তনবাদের পার্থক্য মূলত এই জায়গাটিতেই।
ছবি। পেজ ১৫৬
চিত্র : অধ্যাপক হয়েল ভেবেছিলেন কতগুলো রাসায়নিক পদার্থ মিলেমিশে হঠাৎ করেই ব্যাকটেরিয়ার মতো জটিল জীবের অভ্যুদয় হওয়াটাই অজৈবজনি (Abiogenesis), কিন্তু সত্যিকার অজৈবজনি কখনোই একধাপে ঘটে না, বরং এটি বিভিন্ন ছোট ছোট ধাপের সম্মিলিত প্রক্রিয়ার ফসল।
‘মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে’ বইয়ে অজৈবজনি তথা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রাণের উদ্ভবের পেছনে বিভিন্ন ধাপগুলো বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। প্রথম জৈবকোষ কেবল চান্সের মাধ্যমে তৈরি হয় নি। প্রথম জৈবকোষ তৈরি হয়েছে ধাপে ধাপে। বিজ্ঞানী ওপারিন[১২৬] আর হালডেন[১২৭] তাঁদের গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, সাড়ে চারশো কোটি বছর আগেকার পৃথিবী কিন্তু কোনো দিক দিয়েই আজকের পৃথিবীর মতো ছিল না। তাঁদের মতে, আদিম বিজারকীয় পরিবেশে একসময় এসব গ্যাসের ওপর উচ্চশক্তির বিকিরণের প্রভাবে নানা ধরনের জৈব রাসায়নিক পদার্থের উদ্ভব হয়। এগুলো পরবর্তীকালে নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়ার মাধ্যমে আরও জটিল জৈব পদার্থ উৎপন্ন করে। এগুলো থেকেই পরবর্তীকালে ঝিল্লি তৈরি হয়। ঝিল্লিবদ্ধ এসব জৈব পদার্থ বা প্রোটিনয়েড ক্রমে ক্রমে এনজাইম ধারণ করতে থাকে আর বিপাক ক্রিয়ার ক্ষমতা অর্জন করে। এটি একসময় এর মধ্যকার বংশগতির সংকেত দিয়ে নিজের প্রতিকৃতি তৈরি করতে ও বা পরিব্যক্তি বা মিউটেশন ঘটাতে সক্ষম হয়। এভাবেই এক পর্যায়ে তৈরি হয় প্রথম আদি ও সরল জীবনের। ওপারিন এবং হালডেন তত্ত্বের বহু স্তরই পরবর্তী গবেষকদের পরীক্ষালব্ধ গবেষণায় (Urey-Miller, 1953[১২৮], 1959[১২৯] Fox 1960[১৩০]; Fox and Dose 1977[১৩১], Cairn Smith 1945[১৩২], de Duve 1995[১৩৩], Russell and Hall 1997[১৩৪]; Wächtershäuser 2000[১৩৫], Smith et al. 1999[১৩৬], Huber et al. 2003[১৩৭] সত্য বলে প্রতীয়মান হয়েছে। বিজ্ঞানীরা আদি জীবকোষ তৈরির পেছনে যে ধাপগুলোকে ইতোমধ্যেই শনাক্ত করেছেন সেগুলো হলো—
ধাপ-১ : জৈব যৌগের উৎপত্তি
হাইড্রোকার্বন উৎপাদন (মুক্ত পরমাণুগুচ্ছ CH এবং CH)-এর বিক্রিয়া, বাষ্পের সাথে মেটালিক কার্বাইডের বিক্রিয়া)
হাইড্রোকার্বনের অক্সি ও হাইড্রক্সি-উপজাতের উৎপাদন (বাষ্প ও হাইড্রোকার্বনের বিক্রিয়ায় এলডিহাইড, কিটোন উৎপাদন)
কার্বোহাইড্রেট উৎপাদন (গড়ুকোজ, ফুকটোজ আর ঘনীভবনের ফলে চিনি, স্টার্চ, গ্লাইকোজেন) ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলের উৎপত্তি (ফ্যাট বা চর্বির ঘনীভবন)। অ্যামাইনো এসিড গঠন (হাইড্রোকার্বন, অ্যামোনিয়া আর পানির বিক্রিয়া)
ধাপ-২ : জটিল জৈব অণুর উৎপত্তি (পলিমার গঠন)
• প্রোটিনযেড মাইক্রোস্ফিয়ার
• কো-অ্যাসারভেট
ধাপ-৩ : পলিনিউক্লিটোইড বা নিউক্লিক এসিড গঠন
ধাপ-৪ : নিউক্লিযোগ্রোটিন গঠন
ধাপ-৫: আদি কোষ বা ইউবায়োন্ট গঠন (কো-অ্যাসারভেটের ভেতরে নিউক্লিযোপ্রোটিন আর অন্যান্য অণু একত্রিত হয়ে লিপোপ্রোটিন ঝিল্লি দিয়ে আবদ্ধ প্রথম কোষ; প্রথম জীবন)
ধাপ-৬ : শক্তির উৎস ও সরববাহ (শক্তির সরবরাহে ঘাটতি দেখা দেওয়ায়, প্রকৃতিতে টিকে রইল তারাই যারা প্রোটিনকে এনজাইমে রূপান্তরিত করে সরল উপাদান থেকে জটিল বস্তু তৈরি করতে পারত, আর সেসব দ্রব্য থেকে শক্তি নির্গত করতে পারত)।
ধাপ-৭ : অক্সিজেন বিপ্লব (অক্সিজেনহীন বিজারকীয় আবহাওয়া অক্সিজেনম জারকীয় আবহাওয়ায় রূপান্তরিত হলো-আজ থেকে দু’শ কোটি বছর আগে)
ধাপ-৮ : প্রকৃত কোষী জীবের উৎপত্তি (প্রোক্যারিওট থেকে ইউক্যারিওট)
ধাপ-৯ : জৈব-বিবর্তন বা বায়োজেনেসিস (জীব থেকে জীবে বিবর্তন)।
এরপরেও বলতে দ্বিধা নেই যে, বিজ্ঞানীরা এখনও এমন কোনো জীবকোষ ল্যাবরেটরিতে তৈরি করতে পারেন নি যা ফ্লাস্কের গা বেয়ে নেমে এসে আমাদের চমকে দেবে। এর একটি প্রধান কারণ ‘সম্য’। জীবকোষ তৈরির পেছনে পৃথিবীতে বিবর্তন প্রক্রিয়া চলেছে কোটি কোটি বছর ধরে। আর এই কোটি বছরে পৃথিবীর আবহাওয়াও বদলেছে বিস্তর। যেমন, আদিম পরিবেশে মুক্ত-অক্সিজেন ছিল না, অক্সিজেনহীন বিজারকীয় আবহাওয়া অক্সিজেনম জারকীয় আবহমণ্ডলে রূপান্তরিত হয় আজ থেকে দুই বিলিয়ন বছর আগে। আবার বর্তমান বিশ্বের বায়ুমণ্ডলে আদিম পরিবেশের মতো মিথেন ও অ্যামোনিয়া নেই, তার জায়গায় আছে জলীয় বাষ্প, কার্বন-ডাই অক্সাইড, আণবিক নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও প্রচুর আণবিক অক্সিজেন। এই কোটি বছরের সম্য-প্রসার আবহমণ্ডলের পরিবর্তনকে ল্যাবরেটরির ফ্লাস্কে বেঁধে রাখা যায় না। কিন্তু ফ্লাস্কে বিবর্তনের সিমুলেশন না করলেও কৃত্রিম উপায়ে প্রাণ তৈরিতে ঠিকই সফল হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। সম্প্রতি ক্রেগ ভেন্টর ভার সিনথেটিক লাইফের গবেষণা থেকে প্রথম কৃত্রিম জীবকোষ তৈরি করতে সমর্থ হয়েছেন[১৩৮]। তিনি প্রাথমিকভাবে ইস্ট থেকে ক্রোমোজোমের বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ করেন, কিন্তু ক্রোমোজোমের পূর্ণাঙ্গ রূপটি কম্পিউটারে সিমুলেশন করে বানানো Mycoplasma mycoides নামের একটি ব্যাকটেরিয়ার জিনোমের অনুকরণে। তারা এটি বানানোর জন্য তৈরি করেন এক বিশেষ ধরনের সফটওয্যার। এই সফটওয়্যারের সাহায্যেই তৈরি করা হয় কৃত্রিম ক্রোমোজোম এবং তাতে সংযুক্ত করা হয় কিছু জলছাপ (এটি আসলে ইমেইল আইডি, ভেন্টরদের দলের সদস্যদের নাম এবং কিছু বাড়তি তথ্য)। এভাবে বানানো ক্রোমোজোমটি পরে পুনঃ স্থাপিত হয় Mycoplasma capricolum নামের একটি সরল ব্যাকটেরিয়ার কোষে, যার মধ্যেকার ক্রোমোজোম আগেই সরিয়ে ফেলা হয়। এভাবেই তৈরি হয় প্রথম কৃত্রিম ব্যাকটেরিয়া নামে কৃত্রিম হলেও আচরণে এটি অবিকল মূল ব্যাকটেরিয়ার (Mycoplasma mycoides) মতোই। শুধু তাই নয়, তাদের তৈরি এই কৃত্রিম ব্যাকটেরিয়াটি স্বাভাবিকভাবে বংশবিস্তারও করছে। সংক্ষেপে এই পদ্ধতিকেই বলা হচ্ছে সিনথেটিক প্রক্রিয়ায় জীবনের বিকাশ ঘটানোর সুদূরপ্রসারী প্রক্রিয়া। এভাবে উপাত্ত সাজিয়ে সরল জীবনের ভিত্তি গড়ে ফেলেছেন তিনি, তৈরি করে ফেলেছেন প্রথম কৃত্রিম জীবনের। তিনি নিজেই বলছেন, এই পদ্ধতিতে এমন একটি ব্যাকটেরিয়া তিনি বানিয়েছেন যার অভিভাবক প্রকৃতিতে পাওয়া যাবে না, কারণ অভিভাবক রয়েছে কম্পিউটারে। প্রাণের উদ্ভব যদি এতই অসম্ভাব্য একটি ব্যাপার হতো, তবে বিজ্ঞানীদের এই ধরনের গবেষণাগুলো কখনোই সফলতার মুখ দেখতো না। এ ছাড়া এর আগের অধ্যায়ে আমরা বেশ কিছু পরিচিত স্বতঃ সংগঠনের উদাহরণের সাথেও পরিচিত হয়েছিলাম। বহু গবেষকই মনে করেন স্বতঃ সংগঠন ব্যাপারটি প্রকৃতির অনিবার্য বাস্তবতা হলে সেলফ সাসটেইনিং বিক্রিয়ায় নেটওয়ার্ক উৎপন্ন হওয়ার মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভাবেই প্রথম প্রাণের উদ্ভব ঘটা সম্ভব।[১৩৯]
সব মিলিয়ে হয়েলের জঞ্জাল থেকে বোয়িং উপমা জীববিজ্ঞানে বহু আগেই প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। খ্যাতনামা জীববিজ্ঞানী জন মায়নার্ড স্মিথ তো স্পষ্ট করেই বলেন, ‘কোনো জীববিজ্ঞানীই হয়েলের মতো চিন্তা করেন না যে, জটিল কাঠামো জঞ্জাল থেকে বোয়িং-এর মতো এক ধাপে হুট করে তৈরি হয়’[১৪০] হয়েলের এই বোয়িং উপমার সমালোচনা সময়ে সময়ে করেছেন স্ট্রাহেলার, ম্যাক্লিভার, কাউফম্যান, দ্য দ্যুভে, পিটার স্কেলটন, রুডলগ রাফ, পেনক, ম্যাট ইং এবং ড্যানিয়েল ডেনেটসহ বহু বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকই। মূলত হয়েলের এই অপরিণামদর্শী উপমাকে এখন অবহিত করা হয়ে থাকে হয়েলের হেত্বাভাস (Hoyel’s fallacy) হিসেবে[১৪১]। রিচার্ড ডকিন্স তার ‘গড ডিলুশন’ বইয়ে রসিকতা করে বলেন, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা জটিল জীবজগতের উদ্ভবের তাও একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাই। কিন্তু ঈশ্বর নামে সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান এক জটিল সম্বা হুট করে কোথা থেকে উদ্ভূত হলো, তার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাই আমরা কোথাও পাই না, কখনও পাবও না। তাই ঈশ্বরই হচ্ছেন হয়েলের ‘আল্টিমেট বোয়িং ৭৪৭,[১৪২]
০৪. শুরুতে?
– পৃথিবী কোথা থেকে এল?
–আমি জানি না। ভাবল সোফি। নিশ্চয়ই কেউ-ই আসলে জানে না সেটা। জীবনে এই প্রথমবারের মতো সে উপলব্ধি করল যে, পৃথিবীটা কোথা থেকে এল এ-ব্যাপারে অন্তত প্রশ্ন না করে পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই ঠিক নয় …
–সোফির জগৎ, ইয়স্তেন গার্ডার
এই সুন্দর ফল, সুন্দর ফল, মিঠা নদীর পানি ছেড়ে এবার তাকানো যাক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দিকে এই সুন্দর চাঁদ, সুন্দর তারা, অসীম শূন্যতার দিকে। বাইবেলের প্রথম বাক্য, ইন দ্য বিগিনিং… বা ‘শুরুতে …’ এবং পরবর্তীকালে আরও অনেকবার মহাবিশ্ব সৃষ্টি সম্পর্কিত বাক্য, কোরআনের বিভিন্ন আয়াত (৪৫ : ৩-৫, ২১ : ৩০, ৪১ : ১১, ২১ : ৩৩, ৫১ : ৪৭ ইত্যাদি) পড়ে আমরা জানতে পারি, এই অপার মহাবিশ্ব একজন মহাপরাক্রমশালী কেউ সৃষ্টি করেছিলেন শূন্য থেকে। বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন ঈশ্বরকে বসিয়েছে সেই স্রষ্টার আসনে। ঈশ্বর ভিন্ন হলেও ধর্মবেত্তাদের আয়াত থেকে উদ্ধার করে আনা দেওয়া যুক্তিগুলো একদম কাছাকাছিঃ
১। প্রতিটি ঘটনারই এক বা একাধিক কারণ রয়েছে।
২। কোনো ঘটনার কারণই সেই ঘটনাটা নিজে নয়।
৩। কোনো একটা ঘটনার কারণ হিসেবে থাকে একটা পূর্ববর্তী ঘটনা। সেই পূর্ববর্তী ঘটনার কারণ হিসেবেও থাকতে পারে তার পেছনের কোনো ঘটনা। কিন্তু এভাবে ঘটনাপ্রবাহ। অনন্তকাল ধরে চলতে পারে না।
৪। ভাই অবশ্যই শুরুর দিকের কোনো ঘটনা প্রবাহের একটি আদি কারণ থাকবে।
৫। আর সেই আদি কারণই ঈশ্বর। অতএব ঈশ্বর আছেন।
আমরা সাধারণভাবে ধরে নেই মহাবিশ্বের একটি সূচনা ছিল। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে, বিগব্যাং নামক এক মহাবিস্ফোরণের ফলে এই সকল কিছুর উৎপত্তি হয়েছে। যেহেতু কোনোকিছুই নিজে নিজে শুরু হতে পারে না, একে অন্য কারও দ্বারা শুরু হতে হয়, সুতরাং ঈশ্বর হলেন সেই ব্যক্তি যিনি বিগব্যাং-এর মাধ্যমে প্রথম বলটা গড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমরা কি তবে। ঈশ্বরকে খুঁজে পেলাম?
যুক্তির প্রথম পয়েন্টটা এমন হওয়া উচিত ছিল যে, সকল কিছু হবার পেছনেই কারণ রয়েছে কিংবা কারণ ছাড়া কোন কিছু তৈরি হতে পারে না।’ সৃষ্টিবাদীদের কথা অনুসারে যদি সকল কিছুর হবার পেছনে একটি কারণ থাকে তাহলে সেটা ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও একইভাবে প্রযোজ্য হবার কথা। মহাবিশ্ব সৃষ্টি করা হয়েছে, সৃষ্টিকর্তা হলেন ঈশ্বর। এবার তাহলে কথা হলো, ঈশ্বরকে সৃষ্টি করল কে? ঈশ্বরবাদীরা এক্ষেত্রে জবাব দেন, ঈশ্বরের কোনো সূচনা নেই, তিনি প্রথম থেকেই এমন ছিলেন, তাকে কেউ সৃষ্টি করেন নি, তিনি নিজে নিজেই হয়েছেন, তারপর খুব দারুণ কিছু ব্যাখ্যা করে ফেলেছেন এমন একটা ভাব ধরেন।
‘যার শুরু আছে তার পেছনে কারণ থাকতেই হবে’-এই ধরনের দর্শন কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের উদাহরণের মাধ্যমে বিজ্ঞান অনেক আগেই বাতিল করে দিয়েছে। আণবিক পরিবৃত্তি (Atomic Transition), আণবিক। নিউক্লিয়াসের তেজস্ক্রিয় অবক্ষয়ের (Radioactive decay of nuclei) মতো কোয়ান্টাম ঘটনাসমূহ ‘কারণবিহীন ঘটনা হিসেবে ইতোমধ্যেই বৈজ্ঞানিক সমাজে স্বীকৃত। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্ব (uncertainty principle) অনুযায়ী সামান্য সময়ের জন্য শক্তি (যা E = mc2 সূত্রের মাধ্যমে শক্তি ও ভরের সমতুল্যতা প্রকাশ করে) উৎপন্ন ও বিনাশ ঘটতে পারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে-কোনো কারণ ছাড়াই। এগুলো সবগুলোই পরীক্ষিত সত্য[১৪৩]। তাই আমরা যদি ধরে নেই প্রাকৃতিক বিশ্ব কোনো কারণ ছাড়া বা অন্য কারও হাত ছাড়াই উদ্ভূত হয়েছে সেক্ষেত্রে অযথা ঈশ্বরকে যোগ করার ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। অক্কামের ক্ষুরের (occam’s razor) মূলনীতি অনুযায়ী অপ্রয়োজনীয় সকল ধারণা কেটে ফেলতে হয়*।[* এ প্রসঙ্গে পড়ুন এই বইয়ের পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ অক্কামের ক্ষুর এবং বাহুল্যময় ঈশ্বর] মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে ঈশ্বরকে নিয়ে আসা একেবারেই অপ্রয়োজনীয়। এই নিয়ে আসার মাধ্যমে আমরা কোনো প্রশ্নেরই জবাব পাই না, উল্টো আরও প্রশ্ন সৃষ্টি করি। [১৪৪]
সৃষ্টিবাদীরা প্রাকৃতিক বিশ্ব এমন কেন, এটা এমন কীভাবে হলো, শুরু যদি হয়েই থাকে তাহলে কে প্রথম কাজটা করল?-এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে দিশেহারা হয়ে একটি বাক্যই উচ্চারণ করেন, ঈশ্বর করেছেন। এখন তাহলে দুর্মুখেরা সেই একই প্রশ্ন আবার করবেন, ঈশ্বরটি কে? তিনি কীভাবে এলেন? যদি এসেই থাকেন তাহলে কে তাকে আনলেন? কথিত আছে, ঈশ্বরের মহাবিশ্ব সৃষ্টি এবং তার অপার মহিমা বর্ণনা করার সময় সেন্ট অগাস্টিনকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, আচ্ছা! মহাবিশ্ব সৃষ্টির আগে ঈশ্বর কী করছিলেন? জবাবে তিনি রেগেমেগে উত্তর দিয়েছিলেন, যারা এই ধরনের প্রশ্ন করে তাদের জন্য জাহান্নাম তৈরি করছিলেন ঈশ্বর।
ঈশ্বরবাদীদের এই উত্তর খুঁজতে গিয়ে আরও বড় প্রশ্নের উদ্ভাবন নিয়ে বার্ট্রান্ড রাসেল একটা চমৎকার গল্পের অবতারণা করেছিলেন। একবার একটা গণসম্মেলনে মহাবিশ্ব নিয়ে লেকচার দেয়ার সময় এক বৃদ্ধা নারী বললেন তার পুরাণ অনুযায়ী মহাবিশ্ব একটি হাতির ওপর, হাতিটি একটি কচ্ছপের ওপর বিশ্রাম নেয়। যখন রাসেল বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তা কচ্ছপটি কার উপর বিশ্রাম নেয়?’ তখন তিনি বলেন, ‘এসো আমরা অন্য কিছু নিয়ে কথা বলি।
না, আজকে আমরা অন্যকিছু নিয়ে কথা বলব না। আমরা এই অন্তিম। প্রশ্নগুলোই করব। শুধু প্রশ্ন উত্থাপন করেই আমরা থেমে যাব না, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলো কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায় সেটাও আলোচনা করব। সব প্রশ্নের জবাব দিতে পারব এ দাবি নিশ্চয় আমরা করব না, কিন্তু এটুকু বলতে পারি, বিজ্ঞানের বৈপ্লবিক অগ্রগতির ফলে আমরা এখন অনেক কিছুরই জবাব দিতে সক্ষম। যেখানে বিজ্ঞান এখনও পৌঁছাতে সক্ষম হয় নি সেখানেই আমরা ঈশ্বরকে বসিয়ে দিয়ে হাত ঝেড়ে ফেলব সেটাও ঠিক নয়। বিজ্ঞানের দর্শন আমাদের বুঝতে হবে। আমরা প্রশ্ন করব, আমরা উত্তর খুঁজব। সেই উত্তর খোঁজার পথটা যৌক্তিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। কেবল বিশ্বাস-নির্ভর উত্তরে আমরা আবদ্ধ থাকব না।
আসুন প্রিয় পাঠক, চোখ মেলে তাকানো যাক মহাবিশ্বের অন্তিম রহস্যগুলোর দিকে।
.
অলৌকিকতা
মহাবিশ্ব কেমন করে এলো? সহস্রবছর ধরে মানুষের মনকে আন্দোলিত করা একটি প্রশ্ন। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় তিনটি ধর্ম ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলাম অনুসারে একজন ঈশ্বর এই মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছিলেন। প্রশ্নটার এটি একটি উত্তর এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি হাইপোথিসিস। হাইপোথিসিস যে কোনো কিছুই হতে পারে। তবে সেটিকে সত্য বা বাস্তবতার পর্যায়ে যাওয়ার জন্য যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে হয়। এই অধ্যায়ে আমরা এই ঈশ্বর হাইপোথিসিসকে বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করব, আমরা খুঁজব অতিপ্রাকৃতিকভাবে মহাবিশ্বের সৃষ্টি হওয়ার হাইপোথিসিসের সত্যতার কোনো প্রমাণ আছে কিনা। যে প্রমাণগুলো আমাদের দরকার তা হলো, ১) মহাবিশ্বের একটি সূচনা ছিল ২) এই সূচনা প্রাকৃতিকভাবে বা এমনি এমনি হয় নি। মহাবিশ্ব সৃষ্টির পুরো প্রক্রিয়ায় কোনো একটি ক্ষেত্রে একটি। অলৌকিক ঘটনা বা মিরাকল ঘটেছিল। অর্থাৎ মহাজাগতিক উপাত্ত বা কসমোলজিক্যাল ডাটা যদি আমাদের এমন তথ্য দেয় যে, সৃষ্টির শুরুতে একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ে প্রাকৃতিক নিয়মের/ সূত্রের লঙ্ঘন ঘটেছিল যা ব্যাখ্যাতীত এবং এই ব্যাখ্যাতীত ঘটনা বা মিরাকলের ফলেই মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছিল তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি ঈশ্বর নামক হাইপোথিসিসটির একটি জোরালো ভিত্তি রয়েছে। হয়ত বা ঈশ্বর যে রয়েছেন সেটারও।
প্রায় শত বছর আগে দার্শনিক ডেভিড হিউম দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহারিক প্রয়োগের ওপর ভিত্তি করে তিন ধরনের মিরাকলের কথা বর্ণনা করেছিলেন। তার দেওয়া সংজ্ঞা থেকে মিরাকল বা অলৌকিকতার যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা পাই তা হলো: মিরাকল হচ্ছে, ১) এমন কোনো ঘটনা। যা প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রাকৃতিক নিয়মের লঙ্ঘন ২) ব্যাখ্যাতীত কিছু ৩) অসম্ভব কিন্তু কাকতালীয় ভাবে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা।
ধরা যাক, নাসা অবজারভেটরির বিজ্ঞানীরা সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখলেন আমাদের সৌরজগতে পৃথিবীর পাশে নতুন একটি গ্রহ উদয় হয়েছে কিংবা একটি অতিকায় হাতি বুধ গ্রহকে কেন্দ্র করে পাক খেয়ে চলেছে। আর আমাদের দিকে তাকিয়ে দাঁত কেলিয়ে হাসছে। পৃথিবীর পাশে একটি গ্রহ নতুন করে উদয় হওয়া অসম্ভব, কেননা এতে করে শক্তির নিত্যতার সূত্রের সরাসরি লঙ্ঘন হবে। ঠিক একইভাবে পদার্থবিজ্ঞান আর জীববিজ্ঞানের সমস্ত নিয়ম নীতিকে তোয়াক্কা করে অক্সিজেন বিহীন। মহাশূন্যে একটা হাতির বুধ গ্রহের চারিদিকে পাক খেতে দেখাও অবাস্তব ব্যাপার। যদি সত্যই এমনটা হয়ে থাকে তাহলে আমরা এই ঘটনাকে মিরাকল বা অতিপ্রাকৃতিক আখ্যায়িত করতে পারি।
ধর্মবেত্তা রিচার্ড সুইনবার্নও প্রাকৃতিক কোনো নিয়মের লঘনকে মিরাকল বলে আখ্যায়িত করেছেন[১৪৫]। তিনি এর সাথে আরও যোগ করেছেন, লঘন কেবল একবার সংগঠিত হলে সেটা হবে মিরাকল। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পয়েন্ট। কারণ কোনো লঙ্ঘন যদি বার বার সংঘটিত হতে থাকে তাহলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেটি ঘটার প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা বের করা সম্ভব। যুক্তিসংগত কারণে, পর্যবেক্ষণে বিজ্ঞান পরিবর্তিত হয়। সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মের নিয়মিত লঙ্ঘন হতে থাকলে বিজ্ঞানীরা জানার চেষ্টা করবেন কেন এমন হচ্ছে এবং এর ব্যাখ্যা বের করার জন্য তারা জীবন দিয়ে দিবেন। অবশ্য বিজ্ঞানের এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই অনেকে আবার একে ব্রাত্য মনে করেন। অনেকটা পাশের বাসার যদুর মতো, যে আদতে কিছুই জানে না, আজকে এক কথা বলে তো কালকে অন্য!
অবশ্য বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেকের ধারণা এমন হলেও, বর্তমানে বিজ্ঞানের জানার পরিধি তাদের অনেকেরই কল্পনাতীত। একই সাথে বিজ্ঞানের অনেক নিয়ম ও সত্যতা সহস্র বছর ধরে অপরিবর্তিত। পদার্থবিজ্ঞানের সাধারণ সূত্রগুলো নিউটনের সময় যেমন ছিল এখনও তাই আছে। বিংশ শতকে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের অভূতপূর্ব উন্নতিতে সেই সূত্রগুলো পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে নাড়াচাড়া করা সবাই এখনও নিউটনিয়ান মৌলিক বিষয়গুলো, যেমন শক্তির নিত্যতার সূত্রের মতো বিষয়ে আগের মতোই ঐক্যমত প্রকাশ করেন। চারশো বছরে ধরে এই সূত্র অপরিবর্তিত[১৪৬]। নিত্যতা এবং নিউটনের গতিসূত্র এখনও আপেক্ষিকতা এবং কোয়ান্টাম মেকানিক্সে ব্যবহৃত হয়। রকেটের কক্ষপথ নির্ণয়ের গাণিতিক হিসেবে এখনও নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র ব্যবহার করা হয়।
এখন, শক্তির নিত্যতা এবং ক্লাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞানের অনেক নিয়ম বা সূত্র সৌরজগৎ ছাড়িয়ে লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত গ্যালাক্সির জন্যও সত্য। যেহেতু বিগব্যাং পরবর্তী তেরো বিলিয়ন বছর ধরে এই নিয়মের সত্যতা সম্পর্কে কারও কোনো সন্দেহ নেই, সুতরাং যেকোনো পর্যবেক্ষণ, যা এই সূত্রগুলোকে মিথ্যা বা ভুল প্রমাণ করে তাকে আমরা সরাসরি মিরাকল আখ্যায়িত করতে পারি।
সন্দেহ নেই, ঈশ্বর যদি আসলেই থেকে থাকেন তাহলে তার একই মিরাকল বার বার ঘটানোর সামর্থ্যও আছে। যাই হোক, আগেই বলেছি, বার বার কোনো ঘটনা ঘটলে এর সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা সম্ভব হয় এবং এইসব তথ্য পর্যালোচনার মাধ্যমে ঠিকই প্রাকৃতিক কোনো ব্যাখ্যা বের করা সম্ভব হয়। কিন্তু যেই ঘটনা একবারই ঘটে সেটা রহস্যাবৃত কাকতালীয়ই রয়ে যায়। ক্রিকেটে ব্যাটসম্যানরা যেমন মাঝে মাঝেই আম্পায়ারের বেনিফিট অফ ডাউট পান-এই পুরো আলোচনায় আমরা ঈশ্বর হাইপোথিসিসকে সেই রকম বেনিফিট অফ ডাউট দিতে চাই এবং মহাবিশ্বের ঈশ্বরের মাধ্যমে সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনার সকল পথ উন্মুক্ত রাখতে চাই। কিন্তু যদি সংজ্ঞা অনুযায়ী অত্যন্ত নিম্নমানের অলৌকিকতার সন্ধানও আমরা আমাদের আলোচনায় না পাই, তাহলে সেক্ষেত্রে ঈশ্বর হাইপোথিসিসকে সরাসরি বাতিল করে দেওয়া সম্ভব; একই সাথে ঈশ্বর নামক ধারণাকে, যিনি আমাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে মিরাকল ঘটানোর জন্য বসে থাকেন।
.
পদার্থের উৎপত্তি
বিংশ শতকের শুরুর দিক পর্যন্ত মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে যে একটি বা বেশ কয়েকটি অলৌকিক ঘটনার প্রয়োজন ছিল তা বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত মানতেন। আমরা জানি মহাবিশ্ব বিপুল পরিমাণ পদার্থ দিয়ে গঠিত। আর পদার্থের ধর্ম হলো এর ভর। বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত ধারণা করা হতো, ভরের সৃষ্টি বা ধ্বংস নেই, এটি শুধু এক রূপ থেকে আরেকরূপে পরিবর্তিত হয়। শক্তির নিত্যতার সূত্রের মতো এটি ভরের নিত্যতার সূত্র। সুতরাং এই বিপুল পরিমাণ ভর দেখে সবাই ধারণা করে নিয়েছিলেন একদম শুরুতে ভর সৃষ্টি হওয়ার মতো অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল, যা সরাসরি ভরের নিত্যতার সূত্রের লঙ্ঘন। এবং এটি ঘটেছিল মাত্র একবারই-মহাবিশ্বের সূচনাকালে।
পদার্থের অনেক সংজ্ঞা আমরা জানি। এর মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয়। ও সহজ সংজ্ঞা হলো-পদার্থ এমন একটি জিনিস যাকে লাথি মারা হলে এটি পাল্টা লাথি মারে। কোনো বস্তুর মধ্যকার পদার্থের পরিমাপ করা যায় এর ভরের সাহায্যে। একটি বস্তুর ভর যত বেশি, তাকে লাথি মারা হলে ফিরিয়ে দেওয়া লাথির শক্তি তত বেশি। বস্তু যখন চলা শুরু করে তখন সেই চলাটাকে বর্ণনা করা হয় মোমেন্টামের মাধ্যমে, যা বেশিরভাগ সময়ই বস্তুর ভর ও বস্তুর যে গতিতে চলছে তার গুণফলের সমান। মোমেন্টাম একটি ভেক্টর রাশি, এর দিক ও বস্তুর গতির দিক একই।
ভর এবং মোমেন্টাম দুইটি জিনিসই পদার্থের আরেকটি ধর্মকে যথাযথভাবে সমর্থন করে যাকে আমরা বলি ইনারশিয়া বা জড়তা। একটি বস্তুর ভর যত বেশি তত এটিকে নাড়ানো কঠিন এবং এটি নড়তে থাকলে সেটাকে থামানো কঠিন। একই সাথে বস্তুর মোমেন্টাম যত বেশি তত একে থামানো কষ্ট, থেমে থাকলে চালাতে কষ্ট। অর্থাৎ বেশি পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন।
বস্তুর গতির আরেকটি পরিমাপযোগ্য ধর্ম হলো এর শক্তি। শক্তি, ভর ও মোমেন্টাম থেকে স্বাধীন কোনো ব্যাপার না, এই তিনটি একই সাথে সম্পর্কিত। তিনটির মধ্যে দুইটির মান জানা থাকলে অপরটি গাণিতিকভাবে বের করা সম্ভব। ভর, মোমেন্টাম এবং শক্তি এই তিনটি রাশি দিয়ে আমরা একটি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকতে পারি। সমকোণী ত্রিভুজটির লম্ব হলো মোমেন্টাম p, ভূমি ভর m আর অতিভুজ শক্তি EI এখন পিথাগোরাসের উপপাদ্য ব্যবহার করে এই তিনটির সম্পর্ক নির্ণয় করা যায়। নিচের ছবিতে দ্রষ্টব্য–
ছবি। পেজ ১৭০
চিত্র : লক্ষ্য করুন, কোনো বস্তু যখন স্থির অবস্থায় থাকে তখন এর মোমেন্টাম শূন্য এবং এর শক্তি ভরের সমান (E=m)। এই শক্তিকে বলা হয়ে থাকে পদার্থের স্থিতি শক্তি। এটাই আইনস্টাইনের বিখ্যাত গাণিতিক সম্পর্ক E=mc2 যেখানে c-এর মান 1*। [* আমরা জানি, আলো প্রতি সেকেন্ডে যায় 300,000 কিলোমিটার (বা ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল)। কাজেই সে হিসাবে প্রতিবছরে (অর্থাৎ ৩৬৫ x ২৪ x ৬০ x ৬০ সেকেন্ড) আলো কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে তা আমরা বের করতে পারি। 9.4605284 x 105 মিটার সেটাকেই ১ আলোকবর্ষ বা 1 light year বলে। কাজেই c=1 light-year per year.] ১৯০৫ সালে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তার এই বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ব প্রকাশ করেন। তিনি প্রমাণ করে দেখান যে, শক্তি থেকে ভরের উৎপত্তি সম্ভব এবং একই সাথে শক্তির মাঝে ভরের হারিয়ে যাওয়া সম্ভব।
স্থির অবস্থায় বস্তুর স্থিতি শক্তি ও ভরের মান সমান। এখন বস্তুটি যদি চলা শুরু করে তখন এর শক্তির মান পূর্ববর্তী স্থিতি শক্তির চেয়ে বেশি। অতিরিক্ত এই শক্তিকেই আমরা বলি, গতিশক্তি। রাসায়নিক ও নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার ফলে গতিশক্তি স্থিতি শক্তিতে রূপান্তরিত হয় যা আদতে বস্তুর ভর[১৪৭]। একই সাথে উল্টো ব্যাপারও ঘটে। ভর বা স্থিতি শক্তিকে রাসায়নিক ও নিউক্লিয় বিক্রিয়ার ফলে গতিশক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব, আর সেটা করে আমরা ইঞ্জিন চালাতে পারি, কিংবা বোমা মেরে সব উড়িয়ে দিতে পারি।
সুতরাং আমরা বুঝতে পারলাম মহাবিশ্বের ভরের উপস্থিতি কোনো ধরনের প্রাকৃতিক নিয়মের লঙ্ঘন করে না। শক্তি থেকে ভর উৎপত্তি সম্ভব একই সাথে ভরের শক্তিতে রূপান্তর হওয়াটাও একেবারে প্রাকৃতিক একটি ব্যাপার। সুতরাং ভর সৃষ্টিজনিত কোনো মিরাকল বা অলৌকিক ঘটনার প্রয়োজন মহাবিশ্ব সৃষ্টির সময় ছিল না। কিন্তু আদিতে শক্তি ভবে এলো কোথা থেকে?
শক্তির নিত্যতা সূত্র বা তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র অনুযায়ী আমরা জানি শক্তিকে অন্য কোথাও থেকে আসতে হবে। ধর্মের সৃষ্টিবাণী সত্য হবে যদি তাত্ত্বিকভাবে এমন প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আজ থেকে তেরো দশমিক সাত বিলিয়ন বছর পূর্বে বিগব্যাং-এর শুরুতে শক্তির নিত্যতার সূত্রের লঘন ঘটেছিল।
কিন্তু পর্যবেক্ষণ থেকে শুরু করে তাত্ত্বিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মোটেও ব্যাপারটি এমন নয়। তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র অনুযায়ী একটি বদ্ধ সিস্টেমে মোট শক্তির পরিমাপ স্থির থাকলেই কেবল শক্তি এক রূপ থেকে অন্য রূপে পরিবর্তিত হয়। দারুণ মজার ব্যাপার হচ্ছে, মহাবিশ্বের মোট শক্তির পরিমাণ শূন্য[১৪৮]! বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং তার ১৯৮৮ সালে সর্বাধিক বিক্রিত বই, কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বা A Brief History of Time এ উল্লেখ করেছেন, যদি এমন একটা মহাবিশ্ব ধরে নেওয়া যায়, যেটা মহাশূন্যে মোটামুটি সমসত্ব, তাহলে দেখানো সম্ভব, যে ঋণাত্মক মহাকর্ষীয় শক্তি এবং ধনাত্মক মহাকর্ষীয় শক্তি ঠিক ঠিক কাটাকাটি যায়। তাই মহাবিশ্বের মোট শক্তি থাকে শূন্য[১৪৯]। বিশেষ করে, পরিমাপের অতি সূক্ষ বিচ্যুতি ধরে নিলেও, ক্ষুদ্র কোয়ান্টাম অনিশ্চয়তার মধ্যে, মহাবিশ্বের গড় শক্তির ঘনত্ব ঠিক ততটাই পাওয়া যায়, যতটা থাকা উচিৎ সবকিছু একটা শূন্য-শক্তির আদি অবস্থা থেকে শুরু হলে।[১৫০]
ধনাত্মক ও ঋণাত্মক শক্তির এই ভারসাম্যের কথা নিশ্চিত করে বিগব্যাং তত্ত্বের বর্তমান পরিবর্ধিত রূপ ইনফ্লেশনারি বিগব্যাং ধারণার সত্যতা[১৫১]। ইনফ্লেশন থিওরি প্রস্তাব করার পর একে নানাভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে। যে কোনো পরীক্ষায় ব্যর্থ বা ভুল ফলাফল প্রদানই এই তত্ত্বকে বাতিল করে দেবার জন্য ছিলো যথেষ্ট। কিন্তু এটি সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে বলেই গবেষকেরা মনে করেন। [১৫২]
সংক্ষেপে মহাবিশ্বে পদার্থ ও শক্তির উপস্থিতি কোনো ধরনের প্রাকৃতিক নিয়মের সাথে সাংঘর্ষিক না। ধর্মীয় সৃষ্টিবাণীগুলো এই মহাবিশ্বের সৃষ্টির পেছনে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের কাল্পনিক গালগপ্প ফেঁদে বসেছে। কিন্তু বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক তত্ব এবং পর্যবেক্ষণগুলো আমাদের দেখাচ্ছে কারও হস্তক্ষেপ নয় বরং একদম প্রাকৃতিকভাবেই এই মহাবিশ্বের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব।
এই উদাহরণের মাধ্যমে আরেকটি বিষয়েও আলোকপাত করা যায়। অনেকেই বলে থাকেন, বিজ্ঞানের ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু বলার সামর্থ্য বা সাধ্য নেই। যদি দেখা যেত, বিজ্ঞানীদের গণনাকৃত ভর-ঘনত্বের (mass density) মান মহাবিশ্বকে একদম শূন্য শক্তি অবস্থা (state of zero energy) থেকে উদ্ভূত হতে যা প্রয়োজন তার মতো আসে নি, সেক্ষেত্রে আমরা নির্দ্বিধায় ধরে। নিতে পারতাম, এখনে অন্য কারও হাত ছিল। সেক্ষেত্রে এমন ধারণা করাটা হতো বিজ্ঞানসম্মত সুকুমার আচরণ। এর ফলে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ না হলেও তিনি যে আছেন বা থাকতে পারেন সেটা একটি ভালো ভিত্তি পেত।
.
শৃঙ্খলার সূচনা
সৃষ্টিবাদের আরেকটি অনুমানও প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের সাথে মেলে না। যদি। মহাবিশ্বকে সৃষ্টিই করা হয়ে থাকে তাহলে সৃষ্টির আদিতে এর মধ্যে কিছুটা হলেও শৃঙ্খলা থাকবে] একটি নকশা থাকবে যেটার নকশাকার স্বয়ং স্রষ্টা। এই যে আদি শৃঙ্খলা, এটার সম্ভাব্যতাকে সাধারণত প্রকাশ করা হয় তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের আকারে। এই সূত্রমতে, কোনো একটা আবদ্ধ সিস্টেমের সবকিছু হয় একইরকম সাজানো-গোছানো থাকবে (এন্ট্রপি স্থির) অথবা সময়ের সাথে সাথে বিশৃঙ্খল হতে থাকবে (অর্থাৎ এন্ট্রপি বা বিশৃঙ্খলা বাড়তেই থাকবে)। একটি সিস্টেমের এই বিক্ষিপ্ততা কমানো যেতে পারে শুধু বাইরে থেকে যদি কেউ সেটাকে গুছিয়ে দেয় তখন। তবে বাইরে থেকে কোনো কিছু সিস্টেমকে প্রভাবিত করলে সেই সিস্টেম আর আবদ্ধ সিস্টেম থাকে না।
তাপগতিবিদ্যার এই দ্বিতীয় সূত্রটি প্রকৃতির অন্যতম একটি মৌলিক সূত্র, যার কখনো অন্যখা হয় না। কিন্তু আমরা চারপাশে তাকালে এলোমেলো অনেক কিছুর সাথে সাথে সাজানো গোছানো অনেক কিছুই দেখি। আমরা একধরনের শৃঙ্খলা দেখতে পাই যেটা প্রকৃতির নিয়মেই (তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র) দিনে দিনে বিশৃঙ্খল হচ্ছে (যেমন তেজস্ক্রিয় পরমাণু ভেঙে বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, অথবা ক্ষয়ে যেতে থাকে পুরনো প্রাসাদ)। তার মানে সৃষ্টির আদিতে নিশ্চয়ই সবকিছুকে একরকম ‘পরম শৃঙ্খলা’ দেওয়া হয়েছিল। প্রকৃতির সকল ক্রিয়া-বিক্রিয়া তাপগতিবিদ্যা মেনে সেই শৃঙ্খলাকে প্রতিনিয়ত বিশৃঙ্খল করে চলেছে। তাহলে শুরুতে এই শৃঙ্খলার সূচনা করল কে?
কে আবার? নিশ্চয়ই সৃষ্টিকর্তা! ১৯২৯-এর আগ পর্যন্ত সৃষ্টিবাদের পেছনে এটাই ছিল অলৌকিক সৃষ্টিবাদীদের এটা একটা শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছিল। কিন্তু সে বছর জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডউইন হাবল পর্যবেক্ষণ করলেন যে গ্যালাক্সিসমূহ একে অপর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে নিজেদের দূরত্বের সমানুপাতিক হারে। অর্থাৎ দুইটা গ্যালাক্সির পারস্পরিক দূরত্ব যত বেশি, একে অপর থেকে দূরে সরে যাওয়ার গতিও তত বেশি। এই পর্যবেক্ষণই বিগ ব্যাং তত্ত্বের সর্বপ্রথম আলামত। আর আমরা জানি, একটা প্রসারণশীল মহাবিশ্ব চরম বিশৃঙ্খলা থেকে শুরু হলেও এর মধ্যে আঞ্চলিক শৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। অর্থাৎ সবকিছু এলোমেলোভাবে শুরু হলেও তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রকে ভঙ্গ না করেও প্রসারণশীল কোনো সিস্টেমের কোনো কোনো অংশে শৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।
ব্যাপারটাকে একটা গৃহস্থালির উঠানের উদাহরণ দিয়ে বর্ণনা করা যায়। ধরুন, যখনই আপনি আপনার বাড়ি পরিষ্কার করেন তখন জোগাড় হওয়া ময়লাগুলো জানালা দিয়ে বাড়ির উঠানে ফেলে দেন। এভাবে যদিও দিনে দিনে উঠানটা ময়লা-আবর্জনায় ভরে যেতে থাকে, ঘরটা কিন্তু সাজানো-গোছানো ও পরিষ্কারই থাকে। এভাবে বছরের পর বছর চালিয়ে যেতে হলে যেটা করতে হবে উঠান সব আবর্জনায় ভরে গেলে আশপাশের নতুন জমি কিনে ফেলতে হবে। তারপর সেসব জমিকেও ময়লা ফেলার উঠান হিসেবে ব্যবহার করলেই হলো। তার মানে এভাবে আপনি আপনার ঘরের মধ্যে একটা আঞ্চলিক শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারছেন কিন্তু এর জন্য বাদবাকি জায়গায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে।
একইভাবে মহাবিশ্বের একটি অংশে শৃঙ্খলা রক্ষা করা যেতে পারে, যদি সেখানে সৃষ্ট এন্ট্রপি (বিশৃঙ্খলা) ক্রমাগতভাবে বাইরের সেই চিরবর্ধনশীল মহাশূন্যে ছুড়ে দেওয়া হয়। ওপরের চিত্রে আমরা দেখি, মহাবিশ্বের সার্বিক বিশৃঙ্খলা তাপগতিবিদ্যা মেনেই ধারাবাহিকভাবে বেড়ে চলেছে[১৫৩]। কিন্তু মহাবিশ্বের আয়তনও আবার বাড়ছে ক্রমাগত। সেই বর্ধিত আয়তন (স্পেস)–কে পুরোপুরি বিশৃঙ্খলা ভরে ফেলতে যে বাড়তি এন্ট্রপি লাগত সেটাই হচ্ছে আমাদের সর্বোচ্চ-সম্ভাব্য-বিশৃঙ্খলা। কিন্তু ওপরের ছবি থেকেই আমরা দেখি বাস্তবে বিশৃঙ্খলার বৃদ্ধির হার ততটা নয়। আর বিশৃঙ্খলার অনুপস্থিতি মানেই শৃঙ্খলা। তাই এই বাড়তি স্থানে অনিবার্যভাবেই শৃঙ্খলার উদ্ভব হচ্ছে, এবং সেটা তাপগতিবিদ্যার কোনো সূত্রকে ভঙ্গ না করেই।
ব্যাপারটাকে এভাবে দেখা যায়। আমরা জানি, কোনো একটা গোলকের (আমরা এখানে মহাবিশ্বকে গোলক কল্পনা করছি) এপি যদি সর্বোচ্চ হয় তাহলে সেই গোলকটা কৃষ্ণগহ্বরে (Black hole) পরিণত হয়। অর্থাৎ ঐ গোলকের আয়তনের একটা ব্ল্যাক হোলই হচ্ছে একমাত্র বস্তু যার এন্ট্রপি ঐ আয়তনের জন্য সর্বোচ্চ। কিন্তু আমাদের এই ক্রমপ্রসারণশীল মহাবিশ্ব তো পুরোটাই একটা কৃষ্ণগহ্বর নয়। তার মানে মহাবিশ্বের এন্ট্রপি (বিশৃঙ্খলা) সম্ভাব্য-সর্বোচ্চের চেয়ে কিছুটা হলেও কম। অর্থাৎ সময়ের সাথে সাথে যদিও বিশৃঙ্খলা বাড়ছে ক্রমাগত, তার পরও আমাদের মহাবিশ্ব। এখনো সম্পূর্ণ বিশৃঙ্খল নয়। কিন্তু একসময় ছিল। একদম শুরুতে।
ধরুন, যদি আমরা মহাবিশ্বের এই প্রসারণকে পেছনের দিকে ১৩৪০ কোটি বছর ফিরিয়ে নিয়ে যাই তাহলে আমরা পৌঁছুব সংজ্ঞাযোগ্য একদম আদিতম সময়ে অর্থাৎ প্লাঙ্ক সময় ৬.৪ x ১০-৪৪ সেকেন্ডে যখন মহাবিশ্ব ছিল ততটাই ক্ষুদ্র যার চেয়ে ক্ষুদ্রতম কিছু স্পেসে থাকতে পারে না। এটাকে বলা হয় প্লাঙ্ক গোলক যার ব্যাসার্ধ হচ্ছে প্লাঙ্ক দৈর্ঘ্যের (১. ৬x১০ ৩৫ মিটার) সমান। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র থেকে যেমন অনুমান করা হয় তখন মহাবিশ্বের মোট এন্ট্রপি এখনকার মোট এন্ট্রপির চেয়ে। তেমনভাবেই কম ছিল। অবশ্য প্লাঙ্ক গোলকের মতো একটা ক্ষুদ্রতম গোলকের পক্ষে সর্বোচ্চ যতটা এন্ট্রপি ধারণ করা সম্ভব তখন মহাবিশ্বের এন্ট্রপি ঠিক ততটাই ছিল। কারণ একমাত্র কোনো ব্ল্যাক হোলের পক্ষেই প্লাঙ্ক গোলকের মতো এতটা ক্ষুদ্র আকার ধারণ করা সম্ভব। আর আমরা জানি, ব্ল্যাক হোলের এপি সব সময়ই সর্বোচ্চ।
ছবি। পেজ ১৭৬
চিত্র: এখানে মহাবিশ্বের সর্বমোট-এন্ট্রপি এবং সর্বোচ্চ-সম্ভাব্য-এপিকে মহাবিশ্বের ব্যাসার্ধের ফাংশন আকারে আঁকা হয়েছে। আমাদের মহাবিশ্ব সব সময়ই নিচের রেখা বরাবর প্রসারিত হবে, এবং সেটাই হচ্ছে। কিন্তু নিচের রেখাঁটি কেবল একটা সময়েই ওপরের রেখার সাথে মিলে যাবে সেটা হচ্ছে মহাবিশ্বের উদ্ভবের সময় (প্লাঙ্ক সময়ে)। নিচের মহাবিশ্বের প্রকৃত এন্ট্রপি সূচক রেখাঁটি ওপরের রেখার (যেটি মহাবিশ্বের সর্বোচ্চ এন্ট্রপি সূচক) সাথে মিলে যাবার অর্থ হলো, সূচনালগ্নে মহাবিশ্বের এন্ট্রপি ছিল। সর্বোচ্চ। কিন্তু যেহেতু মহাবিশ্ব ক্রমপ্রসারমাণ, তাই মহাবিশ্বের সর্বোচ্চ এন্ট্রপি তার প্রকৃত এন্ট্রপির চেয়ে দ্রুত হারে বাড়ছে, আর তার ফলে বাড়তি স্থানে মহাবিশ্বের কোনো কোনো অংশে শৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে, তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র ভঙ্গ না করেই (ছবির উৎস: ভিক্টর স্টেঙ্গর, গড দ্য ফেইল্ড হাইপোথিসিস, ২০০৭)।
অনেকে এই তত্ব শুনে অনেক সময়ই যে আপত্তি জানান সেটা হলো, ‘আমাদের হাতে এখনো প্লাঙ্ক সময়ের পূর্বের ঘটনাবলির ওপর প্রয়োগ করার মতো কোনো কোয়ান্টাম মহাকর্ষের তত্ব নেই। আমরা যদি সময়ের। আইনস্টাইনীয় সংজ্ঞাটাই গ্রহণ করি, মানে ঘড়ির সাহায্যে যেটা মাপা হয়। তাহলে দেখা যায় প্লাঙ্ক সময়ের চেয়ে ক্ষুদ্রতম সময়ের ব্যাপ্তি মাপতে হলে আমাদের প্লাষ্ণ দৈর্ঘ্যের চেয়ে ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্যে মাপজোক করতে হবে। যেখানে প্লাঙ্ক দৈর্ঘ্য হচ্ছে প্লাঙ্ক সময়ে আলো যে পথ অতিক্রম করে তার দৈর্ঘ্য। অর্থাৎ আলোর গতি ও প্লাঙ্ক সময়ের গুণফল। কিন্তু হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি থেকে আমরা জানি, কোনো বস্তুর অবস্থান যত সূক্ষভাবে মাপা হয় তার শক্তির সম্ভাব্য মান ততই বাড়তে থাকে। এবং গাণিতিক হিসাব থেকে দেখানো যায় প্লাঙ্ক দৈর্ঘ্যের সমান কোনো বস্তুকে পরিমাপযোগ্যভাবে অস্তিত্বশীল হতে হলে তার শক্তি এতটাই বাড়তে হবে যে সেটা তখন একটা ব্ল্যাক হোলে পরিণত হবে। যে ব্ল্যাক হোল থেকে কোনো তথ্যই বের হতে পারে না। এখান থেকে বলা যায় প্লাঙ্ক সময়ের চেয়ে ক্ষুদ্রতম কোনো সময়ের বিস্তার সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়।[১৫৪]
বর্তমান সময়ের কথা চিন্তা করুন। পদার্থবিজ্ঞানের কোনো প্রতিষ্ঠিত সূত্র প্রযোগেই আমাদের দ্বিধার কিছু নেই যতক্ষণ না আমরা প্লাঙ্ক সময়ের চেয়ে ক্ষুদ্র বিস্তারের কোনো সময়ের জন্য এটার প্রয়োগ করছি। মূলত সংজ্ঞা অনুযায়ী সময়কে গণনা করা হয় প্লাঙ্ক সময়ের পূর্ণ সংখ্যার গুণিতক হিসেবে। আমরা আমাদের গাণিতিক পদার্থবিজ্ঞানে সময়কে একটা ক্রমিক চলক হিসেবে ধরে পার পেয়ে যাই, কারণ সময়ের এই ক্ষুদ্র অবিভাজ্য একক এতই ছোট যে ব্যবহারিক ক্যালকুলাসে আমাদের এর কাছাকাছি আকারের কিছুই গণনা করতে হয় না। আমাদের সূত্রগুলো প্লাঙ্ক সময়ের মধ্যেকার অংশগুলো দিয়ে এক্সট্রাপোলেটেড হয়ে যায় যদিও এই পরিসীমার মধ্যে কিছু পরিমাপ অযোগ্য এবং অসংজ্ঞায়িত হিসেবে থেকে যাবে। এভাবে এক্সট্রাপোলেট যেহেতু আমরা এখন’ করতে পারি, সেহেতু নিশ্চয় বিগ ব্যাং এর শুরুতে প্রথম প্লাঙ্ক পরিসীমার শেষেও করতে পারব।
সেই সময়ে আমাদের এক্সট্রাপোলেশনের হিসাব থেকে আমরা জানি যে তখন এপি ছিল সর্বোচ্চ[১৫৫]। এর মানে সেখানে ছিল শুধু ‘পরম
বিশৃঙ্খলা। অর্থাৎ, কোনো ধরনের শৃঙ্খলারই অস্তিত্ব ছিল না। তাই, শুরুতে মহাবিশ্বে কোনো শৃঙ্খলাই ছিল না। এখন আমরা মহাবিশ্বে যে শৃঙ্খলা দেখি তার কারণ, এখন বর্ধিত আয়তন অনুপাতে মহাবিশ্বের এন্ট্রপি সর্বোচ্চ নয়।
সংক্ষেপে বললে, আমাদের হাতের কসমোলজিক্যাল উপাত্ত মতে মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছে কোনো ধরনের শৃঙ্খলা, পরিকল্পনা বা নির্মাণ ছাড়াই। শুরুতে ছিল শুধুই বিশৃঙ্খলা
বাধ্য হয়েই আমাদের বলতে হচ্ছে যে আমরা চারপাশে যে সূক্ষাতিসূক্ষ শৃঙ্খলা দেখি তা কোনো আদি স্রষ্টার দ্বারা সৃষ্ট নয়। বিগ ব্যাং-এর আগে কী হয়েছে তার কোনো চিহ্নই মহাবিশ্বে নেই। এবং সৃষ্টিকর্তার কোনো কাজের চিহ্নই বা তার কোনো নকশাই এখানে বলব নেই। তাই তার অস্তিত্বের ধারণাও অপ্রয়োজনীয়।
আবারও আমরা কিছু বৈজ্ঞানিক ফলাফল পেলাম যেগুলো একটু অন্যরকম হলেই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রমাণ হয়তো হতে পারত। যেমন মহাবিশ্ব যদি ক্রমপ্রসারণশীল না হয়ে স্থির আকৃতির হতো (যেমনটা বাইবেল বা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলো বলে) তাহলেই তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র মতে আমরা দেখতাম সৃষ্টির আদিতে এন্ট্রপির মান সর্বোচ্চ-সম্ভাব্য এন্ট্রপির চেয়ে কম ছিল। তার মানে দাঁড়াত মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছে খুবই সুশৃঙ্খল একটা অবস্থায় যে শৃঙ্খলা আনা হয়েছে বাইরে থেকে। এমনকি পেছনের দিকে অসীম অতীতেও যদি মহাবিশ্বের অস্তিত্ব থাকত তাহলে আমরা যতই পেছনে যেতাম দেখতাম সবকিছুই ততই সুশৃঙ্খল হচ্ছে এবং আমরা একটা পরম শৃঙ্খলার অবস্থায় পৌঁছে যেতাম যে শৃঙ্খলার উৎস। সকল প্রাকৃতিক নিয়মকেই লঙ্ঘন করে।
.
মহাবিশ্বের সূচনা
বিগব্যাং বা মহাবিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে এই মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছে বিজ্ঞানের এই আবিষ্কারের পর ধর্মবেত্তারা বলা শুরু করেছেন এই আবিষ্কারের ফলেই প্রমাণিত হলো ঈশ্বর আছেন, তাদের ধর্মগ্রন্থে আছে বিগব্যাং-এর কথা!
১৯৭০ সালে জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এবং গণিতবিদ রজার পেনরোজ, পেনরোজের আগের একটি উপপাদ্যের আলোকে প্রমাণ করেন যে, বিগব্যাং-এর শুরুতে ‘সিংগুলারিটি’-র অস্তিত্ব ছিল[১৫৬]। সাধারণ আপেক্ষিকতাকে শূন্য সময়ের আলোকে বিবেচনা করার মাধ্যমে দেখা যায় যে, বর্তমান থেকে পেছনে যেতে থাকলে মহাবিশ্বের আকার ক্রমশ ছোট এবং ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। পেছনে যেতে যেতে যখন মহাবিশ্বের আকার শূন্য হয় তখন সাধারণ আপেক্ষিকতার গণিত অনুযায়ী এর ঘনত্ব হয় অসীম। মহাবিশ্ব তখন অসীম ভর ও ঘনত্ব বিশিষ্ট একটি বিন্দু যার নাম ‘পয়েন্ট অফ সিংগুলারিটি’ বা অদ্বৈত বিন্দু ধর্মবেত্তাদের মধ্যে যারা বিগব্যাংকে ঈশ্বরের কেরামতি হিসেবে ফুটিয়ে তুলতে চান তারা বলেন, তখন সময় বলেও কিছু ছিল না।
তারপর থেকে এভাবেই চলছে। বিগব্যাং-এর আগে অসীম ভর ও ঘনত্বের বিন্দুতে সবকিছু আবদ্ধ ছিল, তখন ছিল না কোনো সময়। তারপর ঈশ্বর ফুঁ দানের মাধ্যমে এক মহাবিস্ফোরণ ঘটান, সূচনা হয় মহাবিশ্বের, সূচনা হয় সময়েরা আমেরিকার রক্ষণশীল লেখক দিনেশ ডি’সুজা তার একটি বইয়ে বলেছেন, ‘বুক অব জেনেসিস যে ঈশ্বরপ্রদত্ত মহাসত্য গ্রন্থ সেটা আরেকবার প্রমাণিত হলো। আধুনিক বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, মহাবিশ্বের উৎপত্তি হয়েছিল শক্তি ও আলোর এক বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে। এমন না যে, স্থান ও সময়ে মহাবিশ্বের সূচনা ঘটেছে, বরং মহাবিশ্বের সূচনা ছিল সময় ও স্থানেরও সূচনা[১৫৭]। ডি’সুজা আরও বলেন, ‘মহাবিশ্বের সূচনার আগে সময় বলে কিছুর অস্তিত্ব ছিল না। অগাস্টিন অনেক আগেই লিখেছিলেন, মহাবিশ্বের সূচনার ফলে সময়ের সূচনা হয়েছিল। এতদিনে আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান নিশ্চিত করল, অগাস্টিন এবং ইহুদি, খ্রিষ্টানদের মহাবিশ্বের সূচনা সম্পর্কে আদিম উপলব্ধির সত্যতা’[১৫৮]। একই ধরনের কথা মুসলিম জগতের জনপ্রিয় ‘দার্শনিক’ হারুন ইয়াহিয়াও (আসল নাম আদনান অকতার; যার নামে বিবর্তন তত্ত্বকে বিকৃত করে সৃষ্টিবাদের রূপকথা প্রচার, নারী ধর্ষণ, মাদক চোরাচালানসহ বহু অভিযোগ আছে, এবং তাকে বিভিন্ন সময় কারাবাসেও যেতে হয়েছিল[১৫৯]) বলেছেন একাধিকবার, প্রাচ্যের খ্রিষ্টীয় সৃষ্টিবাদীদের ধারণাগুলোর পর্যাপ্ত ‘ইসলামীকরণ” করে:
‘বিজ্ঞানীরা এখন জানেন, মহাবিশ্বের উদ্ভব ঘটেছে সিংগুলারিটি থেকে এক অচিন্তনীয় মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে, যাকে আমরা বিগ ব্যাং নামে চিনি। অন্য কথায় মহাবিশ্ব সৃষ্ট হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহই একে বানিয়েছে।
ইসলামি পণ্ডিত জাকির নায়েকও প্রায়ই তার বিভিন্ন লেকচারে কোরআনের একটি বিশেষ আয়াতকে বিগ ব্যাং-এর প্রমাণ হিসেবে হাজির করেন।[১৬০] ডি’সুজা, হারুন ইয়াহিয়া, আর জাকির নায়েকরা সুযোগ পেলেই এভাবে বিগ ব্যাং-এর সাথে নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থের আয়াত জুড়ে দিয়ে এর
একটা অলৌকিক মহিমা প্রদান করতে চান। কিন্তু আদতে বিজ্ঞানের এই আবিষ্কার প্রাচীন এ সমস্ত ধর্মগ্রন্থের সত্যতার কোনো রকমের নিশ্চয়তা তো দেয়ই না, বরং এই ধর্মগ্রন্থ এবং আরও অনেক ধর্মগ্রন্থে থাকা সৃষ্টির যে গল্প এত দিন ধার্মিকেরা বিশ্বাস করে এসেছেন তা কতটা ভুল এবং অদ্ভুত সেটাই প্রমাণ করে।[১৬১]
যাই হোক, সিংগুলারিটির কথা বলে ধর্মবেত্তাদের ভেতরে গভীর সাড়া ফেলা স্টিফেন হকিং এবং পেনরোজ প্রায় বিশ বছর আগে ঐক্যমতে। পৌঁছান যে, বাস্তবে সিংগুলারিটি নামের কোনো পয়েন্টের অস্তিত্ব ছিল না এবং নেই। সাধারণ আপেক্ষিকতার ধারণায় হিসাব করলে অবশ্য তাদের আগের হিসেবে কোনো ভুল ছিল না। কিন্তু সেই ধারণায় সংযুক্ত হয় নি কোয়ান্টাম মেকানিক্স। আর তাই সেই হিসাব আমলে নেওয়া যায় না। ১৯৪৮ সালে হকিং এ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম বইতে বলেন, ‘There was in fact no singularity at the beginning of universe. অর্থাৎ মহাবিশ্বের সূচনার সময়ে সিংগুলারিটির অস্তিত্ব ছিল না।[১৬২]
ডি’সুজা, হারুন ইয়াহিয়া কিংবা জাকির নায়েকের মতো মানুষেরা ‘আ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম’ বইটিতে একনজর চোখ বুলিয়েছেন সেটা সত্যি। কিন্তু পড়ে বোঝার জন্য নয়। তাঁরা খুঁজেছেন তাঁদের মতাদর্শের সাথে যায় এমন একটি বাক্য এবং সেটা পেযেই বাকি কোনো দিকে নজর না দিয়ে লাফিয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন সময় হকিংকে উদ্ধৃত করে বলেন, ‘মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে একটা বিন্দু (সিংগুলারিটি) থেকে বিগ ব্যাং-এর মাধ্যমে[১৬৩]। তাঁরা মূলত হকিং-এর কথার আংশিক উদ্ধৃত করেন, মূল বিষয়টা চেপে গিযে। উদ্ধৃতির সামনের পেছনের বাকি বাক্যগুলোকে উপেক্ষা করার মাধ্যমে এমন একটি অর্থ তাঁরা দাঁড় করান, যা আসলে হকিংযের মতের ঠিক উল্টো। হকিং আসলে বলছিলেন তাঁদের ১৯৭০-এ করা প্রাথমিক এক হিসাবের কথা, যেখানে তাঁরা সিংগুলারিটির কথা আলোচনা করেছিলেন। সম্পূর্ণ কথাটি ছিল এমন] ‘আমার ও পেনরোজের গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল ১৯৭০ সালে একটি যুগ্ম প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রথম প্রকাশিত হয়, যেখানে আমরা প্রমাণ করে দেখাই যে, বিগ। ব্যাং-এর আগে অবশ্যই সিংগুলারিটির অস্তিত্ব ছিল, যতক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব সঠিক বলে ধরে নেওয়া হয়, এবং এ-ও ধরে নেওয়া হয় যে, বর্তমানে মহাবিশ্বে যেই পরিমাণ পদার্থ রয়েছে আগেও তাই ছিল[১৬৪]। হকিং আরও বলেন–
এক সময় আমাদের (হকিং এবং পেনরোস) ভত্ব সবাই গ্রহণ করে নিল এবং আজকাল দেখা যায় প্রায় সবাই এটা ধরে নিচ্ছে যে মহাবিশ্বের উৎপত্তি হয়েছে একটা বিন্দু (সিংগুলারিটি) থেকে বিগব্যাং-এর মাধ্যমে। এটা হয়ত একটা পরিহাস যে এ বিষয়ে আমার মত পাল্টানোর পরে আমিই অন্য পদার্থবিজ্ঞানীদের আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করছি, যে এমন কোনো সিংগুলারিটি আসলে ছিল না-কারণ, কোয়ান্টাম ইফেক্টগুলো হিসেবে ধরলে এই সিংগুলারিটি আর থাকে না।[১৬৫]
অথচ ধর্মবেত্তারা আজ অবধি সেই সিংগুলারিটি পয়েন্টকে কেন্দ্র করে স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণবিষয়ক অসংখ্য বই লিথে চলছেন। বছর খানেক আগে প্রকাশিত বইয়ে র্যাভি জাকারিয়াস বলেন, ‘আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের পাশাপাশি বিগব্যাং তত্ত্বের মাধ্যমে আমরা এখন নিশ্চিত-সবকিছুর অবশ্যই একটি সূচনা ছিল। সকল ডাটা আমাদের এই উপসংহার দেয় যে, একটি অসীম ঘনধের বিন্দু থেকেই মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ শুরু হয়েছিল[১৬৬]।
স্টিফেন হকিংয়ের প্রথম প্রবন্ধ এত ভালোভাবে পড়লেও পরবর্তীকালে আর কিছু পড়ে দেখার ইচ্ছে হয়ত তাদের হয় নি। কিংবা পড়লেও নিজেদের মতের সাথে মেলে না বলে তারা সেটা এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে বের করে দিয়েছেন আরেক কান দিয়ে। তারা অবিরাম ঘেঁটে চলছেন সেই পুরনো কাসুন্দি, যেই কাসুন্দি আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করেছেন কাসুন্দি প্রস্তুতকারী মানুষটি নিজেই।
‘বিগব্যাং তত্ত্বটি বৈজ্ঞানিক সমাজে গৃহীত হওয়ার পর ১৯৫১ সালে Pope Pius XII পন্টিফিক্যাল অ্যাকাডেমির সভায় ঘোষণা করেছিলেন–
যদি সৃষ্টির শুরু থাকে, তবে অবশ্যই এই সৃষ্টির একজন স্রষ্টাও রয়েছে, আর সেই স্রষ্টাই হলেন ঈশ্বর।
এই কারণেই জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং ধর্মযাজক জর্জ হেনরি লেমিত্রি (যিনি ‘বিগব্যাং’ প্রতিভাসের একজন অন্যতম প্রবক্তা) পোপকে সেসময় বিনযের সঙ্গে এধরনের যুক্তিকে ‘অভ্রান্ত হিসেবে প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কেন দিয়েছিলেন সেটা এখন আমরা ঠিকই বুঝতে পেরেছি। পোপ বুঝতে পারেন নি, আর তাই এখন পোপের সময় এসেছে ঈশ্বরের বাণীকে পরিবর্তন করে বিগব্যাং-এর মূল বিষয়ের সাথে ধর্মগ্রন্থকে খাপ খাওয়ানোর।
.
প্রাকৃতিকভাবে কীভাবে মহাবিশ্বের সূচনা হতে পারে
মহাবিশ্বের একটি সূচনা থাকতেই হবে এমন কিন্তু কোনো কথা নেই। একে পেছনে সীমাহীন অনন্ত সময় পর্যন্ত টেনে নেওয়া সম্ভব, যেমন সম্ভব সামনের দিকে অনন্ত সময় পর্যন্ত যাওয়া অর্থাৎ এর কোনো ধ্বংসও নেই। আজ থেকে হাজার কোটি বছর পরে হতে পারে মহাবিশ্বের আর কোনো প্রাণ। তো দূরের কথা জীবজগতের হয়তো কিছুই অবশিষ্ট রইবে না, কিন্তু নিউট্রিনো দিয়ে তৈরি একটা ঘড়ি কিন্তু তখনও চলবে-টিক টিক করে। আর লিন্ডের ‘চিরন্তন’ স্ফীতি ভত্ব, যেটাকে এই মুহূর্তে মহাবিশ্বের অস্তিত্ব ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সবচেয়ে অগ্রগামী তত্ব হিসেবে বিবেচনা হয়, সেটি ‘মহাবিশ্বের সূচনা’ কে খুব জোরেশোরে প্রশ্নবিদ্ধ করে দিয়েছে বলা যায়। তার তত্ব অনুযায়ী এ ধরনের স্ফীতি অবিরামভাবে স্ব-পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে প্রতি মুহূর্তেই তৈরি করছে এবং করবে নতুন নতুন মহাবিশ্ব। এই প্রক্রিয়া অনন্তকাল ধরে অতীতে যেমন চলেছে,ভবিষ্যতেও চলবে অবিরামভাবেই[১৬৭]।
সে হিসেবে ১৪০০ কোটি বছর আগে ঘটা বিগ ব্যাং আমাদের মহাবিশ্বের শুরু হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও অন্য সব মহাবিশ্বের জন্য সেটি ‘শুরু’ নয়। আসলে এই অনন্ত মহাবৈশ্বিক সিস্টেমের কোনো শুরু নেই,শেষও নেই। আজ থেকে ১০০ বিলিয়ন কিংবা ১০০ ট্রিলিয়ন বছর আগে কিংবা পরে যে সময়েই যাওয়া হোক না কেন, স্ফীতির মাধ্যমে ‘মাল্টিভার্স’ তৈরির চলমান প্রক্রিয়া অতীতে যেমন ছিল, ভবিষ্যতেও তেমনি থাকবে। আর এটা গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে খুবই সম্ভব।[১৬৮]
মাল্টিভার্সের ব্যাপারটি যদি বাদও দেই, কেবল আমাদের মহাবিশ্বকে গোনায় ধরলেও এর সূচনার ক্ষেত্রেও অতিপ্রাকৃতিক কোন কিছুর কাছে দ্বারস্থ হবার কোন প্রয়োজন আমাদের নেই। স্রেফ প্রাকৃতিক উপায়েই মহাবিশ্বের সূচনা সম্ভব। প্রাকৃতিক উপায়ে অর্থাৎ, ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে শূন্য থেকে মহাবিশ্ব থেকে উৎপন্ন হতে পারে এ ধারণাটি এ ধারণাটি প্রথম ব্যক্ত করেছিলেন নিউ ইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক এডওয়ার্ড ট্রিয়ন ১৯৭৩ সালে ‘নেচার’ নামক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জার্নালে[১৬৯]। কেন এভাবে, মানে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে মহাবিশ্বের উদ্ভব ঘটল? এর উত্তরে ট্রিয়ন বলেছিলেন, ‘আমি এক্ষেত্রে একটা বিনয়ী প্রস্তাবনা হাজির করতে চাই যে, আমাদের মহাবিশ্ব হচ্ছে এমন একটি জিনিস যেটা কিনা সময় সময় উদ্ভূত হয়। তবে ‘নেচার’ জার্নালে প্রকাশিত। ‘ইজ দ্য ইউনিভার্স এ ভ্যাকুয়াম ফ্লাকচুয়েশন’ শিরোনামের সেই প্রবন্ধে যেভাবে মহাবিশ্ব উৎপত্তি হয়েছে বলে ট্রিয়ন ধারণা করেছিলেন, তাতে কিছু সমস্যা ছিল। প্রথমত: এই প্রক্রিয়ায় ১৪০০ কোটি বছর আগেকার মহাবিশ্বের উদ্ভবের সম্ভাবনাটি খুবই কম। কারণ ফ্লাকচুয়েশনগুলো সাধারণত। হয় খুবই অস্থায়ী। সে হিসাবে একটি ফ্লাকচুয়েশন প্রায় ১৪০০ কোটি বছর। টিকে থাকার সম্ভাবনা প্রায় অসম্ভব ব্যাপারই বলতে হবে। আসলে ফ্লাকচুয়েশনের স্থায়িত্ব বা জীবনকাল নির্ভর করে এর ভরের ওপর ভর যত বড় হবে, ফ্লাকচুয়েশনের জীবনকাল তত কম হবে। দেখা গেছে একটি ফ্লাকচুয়েশনকে তের শ কোটি বছর টিকে থাকতে হলে এর ভর ১০-৬৫ গ্রামের চেয়েও ছোট হতে হবে, যা একটি ইলেকট্রনের ভরের ১০৩৮ গুণ ছোট। আর দ্বিতীয়ত এই মহাবিশ্ব যদি শূন্যাবস্থা (empty space) থেকে উৎপত্তি হয়ে থাকে, তবে প্রশ্ন থেকে যায়, আদিতে সেই শূন্যাবস্থাই বা এল কোথা থেকে (আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী, স্পেস বা শূন্যাবস্থাকে দেশকালের বক্রতার পরিমাপে প্রকাশ করা হয়। প্রথম সমস্যাটির সমাধান ট্রিয়ন নিজেই দিয়েছিলেন। ট্রিষন আপেক্ষিক তত্ব বিশেষজ্ঞদলের (যেমন পদার্থবিদ পিটার বার্গম্যান) সাথে সে সময়ই আলোচনা করে বুঝেছিলেন, একটি আবদ্ধ মহাবিশ্বে ঋণাত্মক মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ধনাত্মক ভর শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। অর্থাৎ মহাবিশ্বে মোট শক্তির পরিমাণ (এবং এই শক্তির সমতুল্য পদার্থের পরিমাণ) শূন্য[১৭০]। সে হিসেবে প্রায় ভরশূন্য অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করলে একটি ফ্লাকচুয়েশন প্রায় অসীম কাল টিকে থাকবে।
১৯৮২ সালে আলেকজান্ডার ভিলেঙ্কিন (Alexander Vilenkin) দ্বিতীয় সমস্যাটির একটি সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেন এভাবে: মহাবিশ্ব সৃষ্ট হয়েছে কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মধ্য দিয়ে আক্ষরিক অর্থেই ‘শূন্য’ থেকে, তবে এই শূন্যাবস্থা শুধু ‘পদার্থবিহীন’ শূন্যাবস্থা নয়, বরং সেইসাথে সময় শূন্যতা এবং স্থান-শূন্যতাও বটে। ভিলেক্ষিন কোয়ান্টাম টানেলিং-এর ধারণাকে ট্রিয়নের তত্বের সাথে জুড়ে দিয়ে বললেন, এ মহাবিশ্ব যাত্রা শুরু। করেছে এক শূন্য জ্যামিতি (empty geometry) থেকে এবং কোয়ান্টাম টানেলিং এর মধ্য দিয়ে উত্তোরিত হয়েছে অশূন্য অবস্থায় (non-empty state) আর অবশেষে ইনফ্লেশনের মধ্য দিয়ে বেলুনের মতো আকারে বেড়ে আজকের অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। [১৭১]
ছবি। পেজ ১৮৬
চিত্র: আলেকজান্ডার ভিলেঙ্কিন তার মডেলের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে শূন্যতা থেকে কোয়ান্টাম টানেলিং-এর মাধ্যমে মহাবিশ্বের উদ্ভব ঘটতে পারে।
ভিলেঙ্কিনের দেওয়া ‘পরম শূন্যের ধারণাটি (absolute nothingness) আত্মস্থ করা আমাদের জন্য একটু কঠিনই বটে! কারণ আমরা শূন্যাবস্থা বা স্পেসকে সব সময়ই পেছনের পটভূমি হিসেবেই চিন্তা করে এসেছি। ব্যাপারটি আমাদের অস্তিত্বের সাথে এমনভাবে মিশে গেছে যে মনের আঙিনা থেকে একে ভাড়ানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। মাছ যেমন জল ছাড়া নিজের অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারে না, ঠিক তেমনি স্পেস ও সময় ছাড়া কোনো ঘটনাপ্রবাহের সংগঠন যেন আমাদের মানস-কল্পনার বাইরে। তবে একটি উপায়ে ‘অ্যাবসোলুট নাথিংনেস’-এর ধারণাটিকে বুঝবার চেষ্টা করা যেতে পারে। যদি পুরো মহাবিশ্বটিকে সসীম আয়তনের একটি আবদ্ধ ক্ষেত্র হিসেবে। চিন্তা করা হয়, এবং এর আয়তন যদি ধীরে ধীরে কমিয়ে শূন্যে নামিয়ে আনা যায়, তবে এই প্রান্তিক ব্যাপারটাকে ‘অ্যাবসোলুট নাথিংনেস’ হিসেবে। ধরে নেওয়া যেতে পারে। আমরা ছবিটিকে আমাদের মানসপটে কল্পনা করতে পারি আর না-ই পারি, ভিলেঙ্কিন কিন্তু প্রমাণ করেছেন, এই শূন্যতার ধারণা গাণিতিকভাবে সুসংজ্ঞায়িত, আর এই ধারণাটিকে মহাবিশ্বের উৎপত্তির গণিত হিসেবে প্রয়োগ করা যেতেই পারে। ভিলেনি তার। ধ্যানধারণা এবং সেই সাথে জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের সামগ্রিক অগ্রগতি নিয়ে সাধারণ পাঠকদের জন্য একটি বই লিখেছেন সম্প্রতি একের ভেতর অসংখ্য–অন্য মহাবিশ্বের সন্ধান শিরোনামে[১৭২]। বইটি বৈজ্ঞানিক তত্বে সমৃদ্ধ কেবল নয়, নানা হাস্যরস এবং কৌতুকসমৃদ্ধ উপাদানেও ভরপুর।
১৯৮১ সালে স্টিফেন হকিং ও জেমস হার্টলি ভিন্নভাবে সমস্যাটির সমাধান করেন। তাঁদের মডেল পদার্থবিজ্ঞানের জগতে ‘প্রান্তহীন প্রস্তাবনা’ (no-boundary proposal) হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে[১৭৩]। তাঁদের মডেলটি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিজ্ঞানী রিচার্ড ফেইনম্যানের বিখ্যাত ইতিহাসের যোগ বা sum over histories’-এর ওপর ভিত্তি করে তৈরি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফেইনম্যান কোয়ান্টাম বলবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে দেখিয়েছিলেন, একটি কণার কেবল একটি ইতিহাস থাকে না, থাকে বিভিন্ন সম্ভাব্য হিস্ট্রির সমাহার, অর্থাৎ গাণিতিকভাবে– অসংখ্য সম্ভাবনার অপেক্ষকের সমষ্টি। আমরা কণার দ্বিচিড় বা ডবল স্লিট এক্সপেরিমেন্টসহ বহু বিখ্যাত পরীক্ষা থেকে ব্যাপারটার সত্যতা জেনেছি। ঠিক একই পদাঙ্ক অনুসরণ করে হকিং দেখিয়েছেন যে, এই ব্যাপারটা আমাদের মহাবিশ্বের জন্যও একইভাবে সত্য মহাবিশ্বেরও কেবল একক ইতিহাস আছে মনে। করলে ভুল হবে, কারণ মহাবিশ্বও কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে সেই কোয়ান্টাম স্তর থেকেই যাত্রা শুরু করেছে। হকিং তার ইউনিভার্স ইন আ নাটশেল’ বইয়ে এ প্রসঙ্গে বলেন, ‘প্রান্তহীন প্রস্তাবনাটা ফেইনম্যানের সেই একাধিক ইতিহাসের ধারণার ওপর ভিত্তি করে তৈরি। কিন্তু ফেইনম্যানের। যোগফলে কণার ইতিহাস এখন স্থলাভিষিক্ত হয়ে গিয়েছে সর্বতোভাবে স্থানকাল দিয়ে, যেটা কিনা মহাবিশ্বের ইতিহাসের সমষ্টি তুলে ধরে’। হকিং ইতিহাসের যোগসূত্র প্রয়োগ করতে গিয়ে আরো দেখলেন, স্থান ও কালের পুরো ব্যাপারটা প্রান্তবিহীন সসীম আকারের বদ্ধ গোলকীয় ক্ষেত্রে পরিণত হয়ে যায়[১৭৪]। ব্যাপারটা যেন অনেকটা পৃথিবীর আকারের সাথে তুলনীয়। আমরা জানি, পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশও আকারে সসীম, কিন্তু প্রান্তবিহীন গোলকের মতো। গোলকের কোনো প্রান্ত থাকে না। সেজন্যই দক্ষিণ মেরুর ১ মাইল দক্ষিণে কী আছে তা বলার অর্থ হয় না। হকিং-এর দৃষ্টিতে মহাবিশ্বের আদি অবস্থাটাও তেমনি। হকিং নিজেই লিখেছেন তার গ্র্যান্ড ডিজাইন’ বইয়ে[১৭৫] :
আমরা যদি আপেক্ষিকতার তত্বের সাথে কোয়ান্টাম তত্বকে মেলাই তাহলে দেখা যায় প্রান্তিক ক্ষেত্রে স্থান–কালের বক্রতা এমন ব্যাপক হতে পারে যে, সময় তখন স্থানের স্রেফ আরেকটা মাত্রা হিসেবেই বিরাজ করে। একদম আদি মহাবিশ্বে, যখন মহাবিশ্ব এতটাই ক্ষুদ্র ছিল যে এর ওপর কোয়ান্টাম তত্ব এবং সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ব উভয়েই কাজ করত তথন আসলে মহাবিশ্বের চারটি মাত্রাই ছিলে স্থানিক মাত্রা এবং কোনো আলাদা সময়ের মাত্রা ছিল না। এর অর্থ, আমরা যখন মহাবিশ্বের ‘সূচনা” সম্পর্কে বলি তখন একটা ব্যাপার এড়িয়ে যাই। সেটা হলো, তখন সময় বলতে আমরা যা বুঝি, তারই কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এটা জানা থাকা প্রয়োজন যে, স্থান ও কাল নিয়ে আমাদের যে প্রচলিত ধারণা, সেটা একদম আদি মহাবিশ্বের ওপর খাটে না। অর্থাৎ সেটা আমাদের অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে, অবশ আমাদের কল্পনা এবং গণিতের ঊর্ধ্বে নয়। এখন, আদি মহাবিশ্বে চারটি মাত্রাই যদি স্থানের মাত্রা হিসেবে কাজ করে তাহলে সময়ের সূচনা হলো কিভাবে?
এই যে ধারণা যে, সময় জিনিসটাও স্থানের আরেকটি মাত্র হিসেবে আচরণ করতে পারে, সেখান থেকে আমরা সময়ের সূচনা বিষয়ক সমস্যাটি কাটিয়ে উঠতে পারি; ঠিক যেভাবে আমরা পৃথিবীর শেষ কোথায় এই প্রশ্নকেও কাটিয়ে উঠি, গোলাকার পৃথিবীর ধারণ মাথায় রেখো মনে করুন, মহাবিশ্বর সূচনা অনেকটা পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুর মতো কেউ যখন সেখান থেকে উত্তর দিকে যেতে থাকে, তখন একই অক্ষাংশের বৃত্তও বড় হতে থাকে, যেটা মহাবিশ্বের আকার ও স্ফীতি হিসেবে ভাবা যায়। তার মানে মহাবিশ্ব শুরু হয়েছে দক্ষিণ মেরুতে, কিন্তু এই দক্ষিণ মেরুবিন্দুর বৈশিষ্ট্য পৃথিবীপৃষ্ঠের আর যেকোনো সাধারণ বিন্দুর মতোই হবে।
এই প্রেক্ষাপটে মহাবিশ্বের সূচনার আগে কী ঘটেছিল, এই প্রশ্নটাই অর্থহীন হয়ে পড়ে। কারণ, এই প্রশ্নটা ‘দক্ষিণ মেরুর দক্ষিণে ক আছে”,এই প্রশ্নের সমতুল। এই চিত্রে মহাবিশ্বের কোনো সীমানা নেই প্রকৃতির যে আইন দক্ষিণ মেরুতে কাজ করে, সেটা অন্য যেকোনে জায়গাতেও কাজ করবে। একই ভাবে, কোয়ান্টাম তত্ত্বে মহাবিশ্বের সূচনার আগে কী ঘটেছিল, এই প্রশ্ন অর্থহীন হয়ে পড়ে। মহাবিশ্বের ইতিহাসও যে সীমানাহীন একটা বদ্ধ তল হতে পারে, এই ধারণাকে বলে ‘নো বাউন্ডারি কন্ডিশন” বা প্রান্তহীনভার শর্ত।
এখানে মূল ব্যাপারটি হলো, হকিং-এর মডেলটিও ভিলেঙ্কিনের মডেলের মতো প্রাকৃতিক ভাবে মহাবিশ্বের উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করতে পারে। তবে হকিং-হার্টলি মডেলের সাথে ভিলেক্ষিনের মডেলের পার্থক্য এই যে, এই মডেলে ভিলেঙ্কিনের মতো ‘পরম শূন্য’র ধারণা গ্রহণ করার দরকার নেই।
ভিলেঙ্কিন ও হকিং-এর এই দুই মডেলের বাইরে আরেকটা মডেল আছে যেটা বাইভার্স (Biverse) নামে পরিচিত। এটা মূলত হকিং-হার্টলি মডেল এবং ভিলেফিনের প্রস্তাবিত মডেল দুটোর একধরনের সমন্বয় বলা যায়। পদার্থবিদ ভিক্টর স্টেঙ্গর এই মডেলের প্রবক্তা[১৭৬]। গাণিতিক মডেল তৈরি করার মাধ্যমে স্টেঙ্গর সম্পূর্ণ ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছেন তার সাইটে এবং পরবর্তীকালে এ নিয়ে তিনি বই ও দার্শনিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।[১৭৭,১৭৮]
ছবি। পেজ ১৮৯
চিত্র: ভিক্টর স্টেরের বাইভার্স মডেল। আমাদের মহাবিশ্ব টানেলিং-এর মাধ্যমে অপর মহাবিশ্ব থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে মনে হবে। কিন্তু অপর মহাবিশ্বের সময়ের দিক আমাদের মহাবিশ্বের সময়ের দিকের ঠিক বিপরীত বলে দুটো মহাবিশ্বই উদ্ভূত হবে আসলে একই ‘আনফিজিকাল রিজন হিসেবে। চিহ্নিত বিশেষ ধরনের শূন্যাবস্থা থেকে।
এই প্রস্তাবনা অনুযায়ী আমাদের মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছিল কোয়ান্টাম টানেলিং প্রক্রিয়ায় অপর একটি মহাবিশ্ব থেকে, যে মহাবিশ্বের অস্তিত্ব ছিল অসীম সময় পর্যন্ত, অন্তত আমাদের সময় পরিমাপের দৃষ্টিকোণ থেকে। কোয়ান্টাম টানেলিং বিজ্ঞানের জগতে একটি প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক ধারণা। সাধারণ ভাষায়, কোনো বস্তুর একটি নিউটনীয় বাধা বা দেয়ালের ভেতর গলে বের হয়ে যাওয়াই কোয়ান্টাম টানেলিং। বিগ ব্যাং-এর মাধ্যমে স্থানের প্রসারণের যে অভিজ্ঞতা আমাদের মহাবিশ্বের অধিবাসীরা উপলব্ধি করেছে, অপর মহাবিশ্বটি উপলব্ধি করবে ঠিক তার উল্টো অর্থাৎ সংকোচনের অভিজ্ঞতা।
আরও একটি ব্যাপার হলো, একটি মহাবিশ্বে সময়ের দিক নির্ধারণ করা হয়ে থাকে এনট্রপি বৃদ্ধি বা বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধির দিকের সাথে সামঞ্জস্য রেখে। সেই শর্তকে সিদ্ধ করতে গেলে অপর মহাবিশ্বের সময়ের দিক আমাদের মহাবিশ্বের সময়ের দিকের ঠিক বিপরীত হতে হবে। আর তাহলেই এই বাইভার্স মডেলে আমাদের মহাবিশ্ব টানেলিং-এর মাধ্যমে অপর মহাবিশ্ব থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে মনে হবে; ঠিক একইভাবে অপর মহাবিশ্বের অধিবাসীদের কাছে মনে হবে তাদের মহাবিশ্ব টানেলিং-এর মাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছে আমাদের মহাবিশ্ব থেকে দুই মহাবিশ্বেরই আপাত উদ্ভব ঘটবে ছবিতে ‘আনফিজিকাল রিজন’ হিসেবে চিহ্নিত বিশেষ ধরনের শূন্যাবস্থা থেকে। গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে মডেলটি ত্রুটিপূর্ণ না হলেও প্রায়োগিক দিক থেকে মডেলটির কিছু জটিলতার কারণে মূলধারার পদার্থবিদদের কাছে এটি জনপ্রিয় নয়।
তবে ভিক্টর স্টেঙ্গর নিজেও স্বীকার করেছেন, আদতে এমনটাই হয়েছে সেটা তিনিও হলফ করে বলতে পারেন না। নিউ এখিজম’ গ্রন্থে তিনি বলেছেন[১৭৯]–
আমার বলতে দ্বিধা নেই, মহাবিশ্বের সূচনা কীভাবে হয়েছিল তা নিয়ে করা আমার ব্যাখ্যা এতটা বিখ্যাত নয় সাধারণের কাছে। অবশ্য, এই প্রস্তাবনা প্রকাশের পর কয়েক বছর কেটে গেলেও এখন পর্যন্ত কোনো পদার্থবিজ্ঞানী, জ্যোতির্বিদ এমনকি দার্শনিকরা কোনো ভুল বের করতে পারেন নি। তারপরও আমি দাবি করি না, ঠিক এইভাবেই মহাবিশ্বের সূচনা হয়েছিল। আমি এতটুকুই বলতে চাই, এটি আমাদের বর্তমান জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি প্রস্তাবনা যার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারি, প্রাকৃতিকভাবে মহাবিশ্বের উৎপত্তি অসম্ভব কোনো ধারণা নয় এবং একই সাথে আমি এটাও বলতে চাই, মহাবিশ্ব সূচনায় আসলে ব্যাখ্যাতীত কোনো বিষয় বা শূন্যস্থান নেই, যেখানে ধর্মবেত্তারা হুট করে ঈশ্বরকে বসিয়ে দিতে পারবেন।
একই ধরনের মনোভাব ব্যক্ত করেছেন এ সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিংও। তিনি তার সাম্প্রতিক গ্র্যান্ড ডিজাইন’ বইয়ে পরিষ্কার করে বলেছেন, বিগব্যাং কোনো স্বর্গীয় হাতের ফসল কিংবা জুক ছিল না। পদার্থবিজ্ঞানের সূত্র মেনেই প্রাকৃতিকভাবে বিগব্যাং-এর মাধ্যমে অনিবার্যভাবে শূন্য থেকে মহাবিশ্ব উদ্ভূত হয়েছে স্বাভাবিক নিয়মেই।[১৮০] বিখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিদ লরেন্স ক্রাউস সম্প্রতি একটি বই। FATC2090– A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather than Nothing[১৮১] শিরোনামে। বইটিতে পদার্থবিদ ক্রাউস পদার্থবিদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন কিভাবে শূন্য থেকে আমাদের চিরচেনা বিপুল মহাবিশ্ব উদ্ভূত হতে পারে একেবারেই প্রাকৃতিক উপায়ে[১৮২]। মূলধারার অধিকাংশ বিজ্ঞানীই এর সাথে আজ একমত পোষণ করেন।
আমরাও মনে করি কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মাধ্যমে মহাবিশ্বের উৎপত্তি এবং তারপর ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের মাধ্যমে একসময় পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তি এবং বিবর্তনের প্রাকৃতিক এবং যৌক্তিক ব্যাখ্যা বিজ্ঞান এই মুহূর্তে আমাদের দিতে পারছে। কাজেই এগুলোর পেছনে ঈশ্বর সম্পর্কিত অনুমান করা স্রেফ বাহুল্য মাত্র।
০৫. আত্মা নিয়ে ইতং বিতং
মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না। কারণ জন্ম নেওয়ার আগে বিলিয়ন বিলিয়ন বছর মৃত থাকার সময় আমার কোনো ধরনের সমস্যা হয় নি।
—মার্ক টোয়েন
আত্মার উৎস সন্ধানে
আত্মার ধারণা অনেক পুরনো। যখন থেকে মানুষ নিজের অস্তিত্ব নিয়ে অনুসন্ধিৎসু হয়েছে, নিজের জীবন নিয়ে কিংবা মৃত্যু নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে, জীবন জগতের বিভিন্ন রহস্যে হয়েছে উদ্বেলিত, তার ক্রমিক পরিণতি হিসেবেই এক সময় মানব মনে আত্মার ধারণা উঠে এসেছে। আসলে জীবিত প্রাণ থেকে জড়জগৎকে পৃথক করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহজ সমাধান হিসেবে আত্মার ধারণা একটা সময় গ্রহণ করে নেওয়া হয়েছিল বলে মনে করা হইয়[১৮৩,১৮৪,১৮৫]। আদিকাল থেকেই মানুষ ইট, কাঠ, পাথর যেমন দেখেছে, ঠিক তেমনিভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে চারপাশের বর্ণাঢ্য জীবজগতকে। ইট, পাথর বা অন্যান্য জড় পদার্থের যে জীবনীশক্তি নেই, নেই কোনো চিন্তা করার ক্ষমতা তা বুঝতে তার সময় লাগে নি। অবাক বিস্মযে সে ভেবেছে তাহলে জীবজগতের যে চিন্তা করার কিংবা চলে ফিরে বেড়ানোর ক্ষমতাটি রয়েছে, তার জন্য নিশ্চয় বাইরে থেকে কোনো আলাদা উপাদান যোগ করতে হয়েছেআয়া নামক অপার্থিব উপাদানটিই সে শূন্যস্থান তাদের জন্য পূরণ করেছে[১৮৬], তারা রাতারাতি পেয়ে গেছে জীবন-মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করার খুব সহজ একটা সমাধান। এখন পর্যন্ত জানা তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, আত্মা দিয়ে জীবন মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা প্রথম শুরু হয়েছিল সম্ভবত নিয়ানডার্থাল মানুষের। আমলে যারা পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে এখন থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ বছর আগে নিয়ানডার্থাল মানুষের আগে পিথেকানথ্রোপাস আর সিনানথ্রোপাসদের মধ্যে এধরনের ধর্মাচরণের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নি। তবে নিয়ানডার্থাল মানুষের বিশ্বাসগুলো ছিল একেবারেই আদিম-আজকের দিনের প্রচলিত ধর্মমতগুলোর তুলনায় অনেক সরল। ইরাকের শানিদার নামের একটি গুহায় নিয়ানডার্থাল মানুষের বেশকিছু ফসিল পাওয়া গেছে যা দেখে অনুমান করা যায় যে, নিয়ানডার্থাল প্রিয়জন মারা গেলে তার আত্মার উদ্দেশ্যে ফুল নিবেদন করত। এমনকি তারা মৃতদেহ কবর দেওয়ার সময় এর সাথে পুষ্পরেণু, খাদ্যদ্রব্য, অস্ত্র সামগ্রী, শিয়ালের দাঁত এমনকি মাদুলিসহ সবকিছুই দিয়ে দিত যাতে পরপারে তাদের আত্মা শান্তিতে থাকতে পারে আর সঙ্গে আনা জিনিসগুলো ব্যবহার করতে পারে। অনেক গবেষক (যেমন নিলসন গেসিটি, রবার্ট হার্টস প্রমুখ) মনে করেন, মৃতদেহ নিয়ে আদি মানুষের পারলৌকিক ধর্মাচরণের ফলেই মানবসমাজে ধীরে ধীরে আত্মার উদ্ভব ঘটেছে।[১৮৭]
.
আত্মা নিয়ে হরেক রকম গপ্প
জীবন মৃত্যুর যোগসূত্র খুঁজতে গিয়ে আত্মাকে ‘আবিষ্কার’ করলেও সেই আত্মা কী করে একটি জীবদেহে প্রাণ সঞ্চার করে কিংবা চিন্তা-চেতনার উন্মেষ ঘটায় তা নিয়ে। প্রাচীন মানুষেরা একমত হতে পারে নি। ফলে জন্ম নিয়েছে নানা ধরনের গালগপ্প, লোককথা আর উপকথার। পরবর্তীকালে এর সাথে যোগ হয়েছে নানা ধরনের ধর্মীয় কাহিনির। জন্ম হয়েছে আধ্যাত্মবাদ আর ভাববাদের, তারপর সেগুলো সময়ের সাথে সাথে আমাদের সংস্কৃতির সাথে মিলেমিশে এমনভাবে একাকার হয়ে গেছে যে আত্মা ছাড়া জীবন-মৃত্যুকে সংজ্ঞায়িত করাই অনেকের জন্য অসম্ভব ব্যাপার। আত্মা নিয়ে কিছু মজার কাহিনি এবারে শোনা যাক।
জাপানিরা বিশ্বাস করে একজন মানুষ যখন ঘুমিয়ে পডে তখন তার ভেতরের আত্মা খুব ছোট পতঙ্গের আকার ধারণ করে তার হা করা মুখ দিয়ে শরীর থেকে বের হয়ে যায়। তারপর যখন ওই ‘আত্মা’ নামক পোকাটি ঘুরে ফিরে আবার হামাগুড়ি দিয়ে মুখ বেয়ে দেহের ভেতরে প্রবেশ করে তখনই ওই মানুষটি ঘুম থেকে জেগে উঠে।[১৮৮] মৃত্যুর ব্যাখ্যাও এক্ষেত্রে খুব সহজ। মুখ দিয়ে বেরিয়ে পোকাটি আর যদি কোনো কারণে ফেলে আসা দেহে ঢুকতে বা ফিরতে না পারে, তবে লোকটির মৃত্যু হয়। অনেক সময় ঘুমন্ত মানুষের অস্বাভাবিক স্বপ্ন দেখাকেও আত্মার অস্তিত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করতেন প্রাচীন মানুষেরা[১৮৯,১৯০]। তারা ভাবতেন, ঘুমিয়ে পড়লে মানুষের আত্মা ‘স্বপ্নের দেশে পাড়ি জমায়। আর তারপর স্বপ্নের দেশ থেকে আবার ঘুমন্ত মানুষের দেহে আত্মা ফেরত এলে মানুষটি ঘুম থেকে জেগে ওঠে। আত্মা নিয়ে এধরনের নানা বিশ্বাস আর লোককথা ইউরোপ, এশ্যিা আর আফ্রিকায় ছড়িয়ে ছিল।
আত্মার এক ধরনের প্রাগৈতিহাসিক ধারণা অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী অ্যাবরোজিনসদের মধ্যে প্রচলিত ছিল[১৯১]। প্রায় চল্লিশ হাজার বছর আগে অ্যাবরোজিনরা অস্ট্রেলিয়ার মূল ভূখণ্ডে আসার পর অনেকদিন বাইরের জগতের সাথে বিচ্ছিন্ন ছিল। ফলে তাদের সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছিল চারপাশের পৃথিবী থেকে একটু ভিন্নভাবে। তাদের আত্মার ধারণাও ছিল বাইরের পৃথিবী থেকে ভিন্ন রকমের। তাদের আত্মা ছিল যোদ্ধা প্রকৃতির। তীর-ধনুকের বদলে বুমেরাং ব্যবহার করত। কোনো কোনো অ্যাবরোজিন এও বিশ্বাস করত যে, তাদের গোত্রের নতুন সদস্যরা আত্মাদের পুনরায় ব্যবহার করতে পারত। ঠিক একইভাবে প্রায় বারো হাজার বছর আগেকার আদিবাসী আমেরিকানদের মধ্যেও আত্মা নিয়ে বিশ্বাস প্রচলিত ছিল, যা প্রকারান্তরে তাদের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধ্যান ধারণার অভিযোনকেই তুলে ধরে। আফ্রিকার কালো মানুষদের মতে সকল মানুষের আত্মার রং কালো। আবার মালযের বহু মানুষের ধারণা, আত্মার রং রক্তের মতোই লাল, আর আয়তনে ভুট্টার দানার মতো। প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের অনেকের ধারণা আত্মা আসলে তরল। অস্ট্রেলিয়ার অনেকে আবার মনে করে আত্মা থাকে বুকের ভেতরে, হৃদয়ের গভীরে; আয়তনে অবশ্যই খুবই ছোট[১৯২]। কাজেই এটুকু বলা যায়, আত্মায় বিশ্বাসীরা নিজেরাই আত্মার সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞার ব্যাপারে একমত নন। আত্মা নিয়ে প্রচলিত পরস্পর বিরোধী বক্তব্যগুলো সেই সাক্ষ্যই দেয়।
ইতিহাস ঘাঁটলে জানা যায়, হিব্রু, পার্সিয়ান আর গ্রিকদের মধ্যে আত্মা নিয়ে বহু ধরনের বিশ্বাস প্রচলিত ছিল। প্রথম দিকে অন্তত খ্রিস্টপূর্ব ছয় শতক পর্যন্ত তো বটেই-হিব্রু, ফোমেনিকানস আর ব্যবিলনীয়, গ্রিক এবং রোমানদের মধ্যে মৃত্যু-পরবর্তী আত্মার কোনো স্বচ্ছ ধারণা গড়ে ওঠেনি। তারা ভাবতেন মানুষের আত্মা এক ধরনের সংজ্ঞাবিহীন ছায়া সদৃশ (Shadowy Entity) অসম্পূর্ণ সত্ত্বা, পূর্ণাঙ্গ কিছু নয়। গবেষক ব্রেমার আত্মা নিয়ে প্রাচীন ধারণাগুলো সম্বন্ধে বলেন, মোটের ওপর আত্মাগুলো ছিল চেতনাবিহীন ছায়া ছায়া জিনিস, পূর্ণাঙ্গ সত্বা তৈরি করার মতো গুণাবলির অভাব ছিল তাতে[১৯৩]।
সম্ভবত জরথ্রুস্ট্র ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যার আত্মা সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনা আধুনিক আধ্যাত্মবাদীদের দেওয়া আত্মার ধারণার অনেকটা কাছাকাছি। জরথ্রুস্ট্র ছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ বছর আগেকার একজন পার্সিয়ান। তার মতানুযায়ী, প্রতিটি মানুষ তৈরি হয় দেহ এবং আত্মার সমন্বযে, এবং আত্মার কল্যাণেই আমরা যুক্তি, বোধ, সচেতনতা এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চা করতে পারি। জরথ্রুস্ট্রবাদীদের মতে, প্রতিটি মানুষই নিজের ইচ্ছানুযায়ী স্বাধীনভাবে কাজ কর্ম করার অধিকারী, এবং সে অনুযায়ী, তার ভালো কাজ কিংবা মন্দ কাজের ওপর ভিত্তি করে তার আত্মাকে পুরস্কৃত করা হবে কিংবা শাস্তি প্রদান করা হবে। জরথ্রুস্ট্রের দেওয়া আত্মার ধারণাই পরবর্তীকালে গ্রিক এথেনীয় দার্শনিকেরা এবং আরও পরে খ্রিস্ট ও ইসলাম ধর্ম তাদের দর্শনের অঙ্গীভূত করে নেয়। খ্রিস্টধর্মে আত্মার ধারণা গড়ে ওঠে সেন্ট অগাস্টিনের হাতে। জরথ্রুস্ট্রের মৃত্যুর প্রায় এক হাজার বছর পর অত্যন্ত প্রভাবশালী ধর্মবেত্তা সেন্ট অগাস্টিন খ্রিস্টধর্মের ভিত্তি হিসেবে একই ধরনের মানুষ = দেহ + আত্মা) যুক্তির অবতারণা করেন। এই ধারণাই পরবর্তীকালে অস্তিত্বের দ্বৈততা (Duality) হিসেবে খ্রিস্ট ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি প্রদান করে। এর সাথে যোগ হয় পাপ-পুণ্য এবং পরকালে আত্মার স্বর্গবাস বা নরকবাসের হরেক রকমের বক্তব্য। এগুলোই পরে ডালপালায় পল্লবিত হয়ে পরে ইসলাম ধর্মেও স্থান করে নেয়। সন্দেহ করা হয়, প্রাথমিকভাবে অগাস্টিন জরথ্রুস্ট্রবাদীদের কাছ থেকেই আত্মার ধারণা পেয়েছিলেন, কারণ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার আগ পর্যন্ত নয় বছর অগাস্টিন ম্যানিকিন (Manchean) গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যাদের মধ্যে জরথ্রুস্ট্রবাদের প্রভাব বিদ্যমান ছিল পুরোমাত্রায়।
হিব্রু এবং গ্রিকদের মধ্যে প্রথম দিকে আত্মা নিয়ে কোনো সংহত ধারণা ছিল না। এই অসংহত ধারণার প্রকাশ পাওয়া যায় হোমারের (খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০) রচনায় ‘সাইকি’ (Psyche) শব্দটির উল্লেখে। হোমারের বর্ণনানুযায়ী, কোনো লোক মারা গেলে বা অচেতন হয়ে পরলে ‘সাইকি’ তার দেহ থেকে চলে যায়। তবে সেই সাইকির সাথে আজকের দিনে প্রচলিত আত্মার ধারণার পার্থক্য অনেক। হোমারের সাইকি ছিল সংজ্ঞাবিহীন ছায়া সদৃশ অসম্পূর্ণ সত্ব; এর আবেগ, অনুভূতি কিংবা চিন্তাশক্তি কিছুই ছিল না[১৯৪]। ছিল না পরকালে আত্মার পাপ-পুণ্যের হিসাব।
এর মাঝে গ্রিসের অযোনীয় যুগের বিজ্ঞানীরা বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হন। ভাববাদের ভাবনা এড়িযে প্রথম যে গ্রিক দার্শনিক জীবনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নিয়ে হাজির হলেন, তার নাম থেলিস (৬২৪-৫৪৭ খ্রি.পূ.)। থেলিসের বক্তব্য ছিল, বস্তু মাত্রই প্রাণের সুপ্ত আধার। উপযুক্ত পরিবেশে বস্তুর মধ্যে নিহিত প্রাণ আত্মপ্রকাশ করে[১৯৫]। পরমাণুবাদের প্রবক্তা ডেমোক্রিটাস (৪৬০-৩৭০ খ্রি.পূ.) প্রাণের সাথে বস্তুর নৈকট্যকে আরও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেন। ডেমোক্রিটাস বলতেন, সমগ্র বস্তুজগৎ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অবিভাজ্য কণা দিয়ে গঠিত। তিনি সে কণিকাগুলোর নাম দিলেন অ্যাটম বা পরমাণু। তিনি শুধু সেখানেই থেমে থাকেন নি, তার পরমাণু তত্বকে নিয়ে গেছেন প্রাণের উৎপত্তির ব্যাখ্যাতেও। তিনি বলতেন, কাদামাটি বা আবর্জনা থেকে যখন প্রাণের উদ্ভব হয় তখন অজৈব পদার্থের অণুগুলো সুনির্দিষ্টভাবে সজ্জিত হয়ে জীবনের ভিত্তিভূমি তৈরি করে। ডেমোক্রিটাসের প্রায় সমসাময়িক দার্শনিক লিউসেপ্লাসও (আনুমানিক ৫০০-৪৪০ খ্রি.পূ.) এধরনের বস্তুবাদী ধারণায় বিশ্বাস করতেন। তিনি বিজ্ঞানে তিনটি নতুন ধারণা চালু করেন চরম শূন্যতা, চরম শূন্যতার মধ্য দিয়ে অ্যাটমের চলাফেরা এবং যান্ত্রিক প্রয়োজন। লিউসেপ্লাসই প্রথম বিজ্ঞানে কার্যকারণ তত্বের জন্ম দেন বলে কথিত আছে[১৯৬]। অযোনীয় যুগের দর্শনের বস্তুবাদী রূপটিকে পরবর্তীকালে আরও উন্নয়ন ঘটান এপিকিউরাস এবং লুক্রেশ্যিস, এবং তা দর্শন ও নীতিশাস্ত্রকেও প্রভাবিত করে। গ্রিক পরমাণুবাদ পরবর্তীকালে বিজ্ঞানকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছিল। যেমন, প্রথম আধুনিক পরমাণুবিদ গ্যাসেন্ডি তার পরমাণুবাদ তৈরির জন্য ঋণ স্বীকার করেছেন ডেমোক্রিটাস এবং এপিকিউরাসের কাছে। গ্রিক পরমাণুবাদ প্রভাবিত করেছিল এরপর পদার্থবিদ নিউটন এবং রসায়নবিদ জন ডালটনকেও তাদের নিজ নিজ পরমাণু তত্ব নির্মাণে।
কাজেই গ্রিসের অযোনীয় যুগে মেইনস্ট্রিম দার্শনিকদের চিন্তা চেতনা ছিল অনেকটাই বস্তুবাদী। কিন্তু পরে পারস্য দেশের প্রভাবে আত্মা-সংক্রান্ত সব আধ্যাত্মিক এবং ভাববাদী ধ্যান-ধারণা গ্রিকদের মধ্যে ঢুকে যায়। ভাববাদী দর্শনের তিন পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন সক্রেটিস, প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল। এরা এথেন্সের সন্তান হলেও সে এথেন্স তখন অবক্ষয়ী এথেন্স। তারপরও পরবর্তী আড়াই হাজার বছর তাদের চিন্তা-চেতনা দিয়ে মানবসমাজ প্রভাবিত হয়েছিল। এদের ক্ষমতার কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, মানব ইতিহাসের প্রথম স্বাধীন নগরের বৈপ্লবিক মহত্ব থেকে তারা মানুষের চিন্তাকে প্রভাবিত করার মতো শক্তিধর হওয়া সত্ত্বেও, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে ক্ষমতাকে তারা প্রতিবিপ্লবের স্বার্থে ব্যবহার করতেন[১৯৭]। তারা গণতন্ত্রের ভয়ে ভীত ছিলেন এবং গণতন্ত্রের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতেন। অযোনীয় যুগের দার্শনিকেরা পলে পলে বস্তুবাদের যে সৌধ গড়ে তুলেছিলেন, তা এই তিন ভাববাদী দার্শনিকের আগ্রাসনে বিলুপ্ত হয়। বস্তুবাদকে সরিযে মূলত রহস্যবাদী উপাদানকে হাজির করে তাঁরা তাঁদের দর্শন গড়ে তোলেন। প্লেটোর বক্তব্য ছিল যে, প্রাণী বা উদ্ভিদ কেউ জীবিত নয়, কেবল যখন আত্মা প্রাণী বা উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করে তখনই তাতে জীবনের লক্ষণ পরিস্ফুট হয়। প্লেটোর এ সমস্ত তত্বকথাই পরে খ্রিস্টধর্মের বুদ্ধিবৃত্তিক সমর্থনের যোগান দেয়। প্লেটোর এই ভাববাদী তত্ব অ্যারিস্টটলের দর্শনের রূপ নিয়ে এরপর হাজার খানেক বছর রাজত্ব করে। এখন প্রায় সব ধর্মমতই দার্শনিক-যুগলের ভাববাদী ধারণার সাথে সংগতি বিধান করে। আত্মা সংক্রান্ত কুসংস্কার শেষ পর্যন্ত মানবসমাজে ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করে।
.
আত্মার অসাড়তা
জীব কী আর জড় কী? বুঝব কী করে কে জীব আর কে জড? জীবিতদের কীভাবে শনাক্ত করা যায়? একটি মৃতদেহ আর একটি জীবিত দেহের মধ্যে পার্থক্যই বা কী? এ প্রশ্নগুলো দিয়ে আগেকার দিনের মানুষের অনুসন্ধিৎসু মন সবসময়ই আন্দোলিত হয়েছে পুরোমাত্রায়। কিন্তু এই প্রশ্নগুলোর কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা না পেয়ে তারা শেষ পর্যন্ত কল্পনা করে নিয়েছে অদৃশ্য আত্মার ভেবেছে আত্মাই বুঝি জীবন ও মৃত্যুর যোগসূত্র। প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের ভাববাদী ধ্যানধারণাগুলো কালের পরিক্রমায় বিভিন্ন ধর্মে জায়গা করে নেওয়ার পর জীবন-মৃত্যুর সংজ্ঞা ধর্মীয় মিথের আবরণে পাখা মেলতে শুরু করল। কল্পনার ফানুস উড়িযে মানুষ ভাবতে শুরু করল, ঈশ্বরের নির্দেশে আজরাইল বা যমদূত এসে প্রাণহরণ করলেই কেবল একটি মানুষ মারা যায়। আর তখন তার দেহস্থিত আত্মা পাড়ি জমায় পরলোকে। মৃত্যু নিয়ে মানুষের এধরনের ভাববাদী চিন্তা জন্ম দিয়েছে আধ্যাত্মবাদের। আধ্যাত্মবাদ স্বতঃ প্রমাণ হিসেবেই ধরে নেয়-আত্মা জন্মহীন, নিত্য, অষ্কয়। শরীর হত হলেও আত্মা হত হয় না। মজার ব্যাপার হলো, একদিকে যেমন আত্মাকে অমর অক্ষয় বলা হচ্ছে, জোর গলায় প্রচার করা হচ্ছে আত্মাকে কাটা যায় না, পোড়ানো যায় না, আবার সেই আত্মাকেই পাপের শাস্তিস্বরূপ নরকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটা, গরম তেলে পোড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ সবই আধ্যাত্মবাদের স্ববিরোধিতা। ধর্মগ্রন্থগুলো ঘাঁটলেই এধরনের স্ববিরোধিতার হাজারও দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে। স্ববিরোধিতা থাকা সত্ত্বেও আত্মার অস্তিত্ব দিয়ে জীবনকে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হয়েছে মানুষ। কারণ সেসময় বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ছিল সীমিত। মৃত্যুর সঠিক কারণ ছিল তাদের জানার বাইরে। সেজন্য অনেক ধর্মবাদীই ‘আত্মা কিংবা ‘মন কে জীবনের আধাররূপী বস্তু হিসেবে কল্পনা করেছেন। যেমন, ইসলাম বলছে, আল্লাহ মানবজাতির সকল আত্মা একটি নির্দিষ্ট দিনে তৈরি করে বেহেস্তে একটি নির্দিষ্ট স্থানে (ইল্লিন) বন্দি করে রেখে দিয়েছেন। আল্লাহর ইচ্ছাতেই নতুন নতুন প্রাণ সঞ্চারের জন্য একেকটি আত্মাকে তুলে নিয়ে মর্ত্যে পাঠানো হয়। আবার হিন্দু আচার্য শঙ্কর তার ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যে বলেছেন, ‘মন হলো আত্মার উপাধি স্বরূপ। ওদিকে আবার সাংখ্যদর্শনের মতে ‘আত্মা চৈতন্যস্বরূপ (সাংখ্যসূত্র ৫/৬৯)। জৈন দর্শনে বলা হয়েছে, ‘চৈতন্যই জীবের লক্ষণ বা আত্মার ধর্ম (ষড়দর্শন সমুচ্চয়, পৃ. ৫০)। স্বামী বিবেকানন্দ পর্যন্ত ভাবতেন, চৈতন্য বা চেতনাই আত্মা’ (বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র, পৃ. ১৬২) স্বামী অভেদানন্দের মতে, ‘আত্মা বা মন মস্তিষ্ক বহির্ভূত পদার্থ, মস্তিষ্কজাত ন্যা’ (মরণের পারে, পৃ. ৯৮)। গ্রিক দর্শনেও আমরা প্রায় একই রকম ভাববাদী দর্শনের ছায়া। দেখতে পাই, যা আগের অংশে আমরা আলোচনা করেছি। অ্যারিস্টটলের পরবর্তী গ্রিক ও রোমান দার্শনিকেরা অ্যারিস্টটলীয় দর্শনকে প্রসারিত করে পরবর্তী যুগের চাহিদার উপযোগী করে তোলেন। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে নয় প্লেটোবাদীরা ‘ঈশ্বর অজৈব বস্তুর মধ্যে জীবন সৃষ্টিকারী আত্মা প্রবেশ করিয়ে দিয়ে তাকে জীবন দান করেন এই মত প্রচার করতে শুরু করেন। নয় প্লেটোবাদী প্লাটিনাসের মতে, ‘জীবনদায়ী শক্তিই জীবনের মূলা’ বস্তুতপক্ষে, জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ‘জীবনশক্তি (Life Force) তত্ব এখান থেকেই যাত্রা শুরু করে এবং জীবনের উৎপত্তি প্রসঙ্গে ভাববাদী দর্শনের ভিত্তিও জোরালো হয়। ধর্মবাদী চিন্তা, বৈজ্ঞানিক অনগ্রসরতা, কুসংস্কার, ভয় সবকিছু মিলে শিক্ষিত সমাজে এই ভাববাদী চিন্তাধারার দ্রুত প্রসার ঘটে।
বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি আর যুক্তির প্রসারের ফলে আজ কিন্তু আত্মা দিয়ে জীবন-মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করার অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলো মানুষের চোখে সহজেই ধরা পড়ছে। যদি জীবনকে ‘আত্মার উপস্থিতি’ আর মৃত্যুকে ‘আত্মার দেহত্যাগ’ দিয়েই ব্যাখ্যা করা হয়, তবে তো যেকোনো জীবিত সত্বরই তা সে উদ্ভিদই হোক আর প্রাণীই হোক আত্মা থাকা উচিত। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে একটি দেহে কি কেবল একটিমাত্র আত্মা থাকবে নাকি একাধিক? যেমন, বেশকিছু উদ্ভিদ গোলাপ, কলা, ঘাসফুল এমনকি হাইড্রা, কোরালের মতো প্রাণীরাও কর্তন (Cut) ও অঙ্কুরোদগমের (Bud) মাধ্যমে বিস্তৃত হয়। তাহলে কি সাথে সাথে আত্মাও কর্তিত হয়, নাকি একাধিক আত্মা সাথে সাথেই অঙ্কুরিত হয়? আবার মাঝে মধ্যেই দেখা যায় যে, পানিতে ডুবে যাওয়া, শ্বাসরুদ্ধ, মৃত বলে মনে হওয়া/ঘোষিত হওয়া অচেতন ব্যক্তির জ্ঞান চিকিৎসার মাধ্যমে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নয় তখন কি দেহত্যাগী আত্মাকেও দেহে ফিরিয়ে আনা হয়? প্রজননকালে পিতৃদত্ত শুক্রাণু আর মাতৃ দত্ত ডিম্বাণুর মিলনে শিশুর দেহকোষ তৈরি হয়। শুক্রাণু আর ডিম্বাণু জীবনের মূল, তাহলে নিশ্চয় তাদের আত্মাও আছে। এদের আত্মা কি তাদের অভিভাবকদের আত্মা থেকে আলাদা? যদি তাই হয় তবে কীভাবে দুটি পৃথক আত্মা পরম্পর মিলিত হয়ে শিশুর দেহে একটি সম্পূর্ণ নতুন আত্মার জন্ম দিতে পারে? মানব মনের এধরনের অসংখ্য যৌক্তিক প্রশ্ন আত্মার অসারত্বকেই ধীরে ধীরে উন্মোচিত করেছে।
আত্মার সংজ্ঞাতেও আছে বিস্তর গোলমাল। কেউ আত্মার চেহারা বায়বীয় ভাবলেও (স্বামী অভেদানন্দের ‘মরণের পারে’ দ্র.) কেউ আবার ভাবেন তরল (প্রশান্ত মহাসাগরের অধিবাসী);কেউ আত্মার রং লাল (মালযের অধিবাসী) ভাবলেও অন্য অনেকে ভাবেন কালো (আফ্রিকাবাসী এবং জাপানিদের অনেকের এধরনের বিশ্বাস রয়েছে)। বিদেহী আত্মার পুনর্জন্ম নিয়ে সমস্যা আরও বেশি। বিশ্বের প্রধান ধর্মমত হিসেবে হিন্দু, ইসলাম এবং খ্রিস্ট ধর্মের কথা আলোচনা করা যাক। হিন্দুরা আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাস করে; আবার অপরদিকে মুসলিম আর খ্রিস্টানদের কাছে আত্মার পুনর্জন্ম বলে কিছু নেই। মজার ব্যাপার হচ্ছে, প্রত্যেকটি ধর্ম তাদের বিশ্বাসকেই অভ্রান্ত বলে মনে করে। এ প্রসঙ্গে প্রবীর ঘোষ তার ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক’ গ্রন্থে বলেন[১৯৯]–
একবার ভাবুন তো, আত্মার চেহারাটা কেমন, তাই নিয়েই বিশ্বের বিভিন্ন দেশবাসীর বিভিন্ন মত। অথচ স্বামী অভেদানন্দই এক জায়গায় বলেছেন, আমাদের মনে রাখা উচিত যে, সত্য কখনও দু’রকমের বা বিচিত্র রকমের হয় না, সত্য চিরকালই এক ও অখণ্ড।
বিবর্তনতত্ত্বের আলোকে মানতে গেলে তো আত্মার অস্তিত্ব এবং পুনর্জন্মকে ভালোমতোই প্রশ্নবিদ্ধ করতে হয়। বিজ্ঞান আজ প্রমাণ করেছে জড থেকেই জীবের উদ্ভব ঘটেছিল। পৃথিবীর বিশেষ ভৌত অবস্থায় নানারকম রাসায়নিক বিক্রিয়ার জটিল সংশ্লেষের মধ্য দিয়ে আর তারপর বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভব ঘটেছে জৈববিবর্তনের বন্ধুর পথে। এই প্রাণের উদ্ভব এবং পরে প্রজাতির উদ্ভবের পেছনে কোনো মন বা আত্মার অস্তিত্ব ছিল না। প্রাণের উদ্ভবের পর কোটি কোটি বছর কেটে গেছে, আর আধুনিক মানুষ তো এলো মাত্র ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার বছর আগে। তাহলে এখন প্রশ্ন হতে পারে পঞ্চাশ হাজার বছর আগে মানুষের আত্মারা কোথায় ছিল? জীবজন্ত কিংবা কীটপতঙ্গ হয়ে? কোন পাপে তাহলে আত্মারা কীটপতঙ্গ হলো? পূর্বজন্মের কোন কর্মফলে এমনটি হলো? পূর্বজন্ম পূর্বজন্ম করে পেছাতে থাকলে যে প্রাণীতে আত্মার প্রথম জন্মটি হয়েছিল সেটি কবে হয়েছিল? হলে নিশ্চয়ই এককোষী সরল প্রাণ হিসেবেই জন্ম নিয়েছিল। এককোষী প্রাণের জন্ম হয়েছিল কোন জন্মের কর্মফলে?
বিবর্তনের আধুনিক তত্ব না জানা সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতের যুক্তিবাদী চার্বাকেরা সেই খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে তাদের সেসময়কার অর্জিত জ্ঞানের সাহায্যে আত্মার অস্তিত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ফেলেছিলেন। আত্মাকে অস্বীকার করার মধ্য দিয়েই সম্ভবত চার্বাকদের লড়াইটা শুরু হয়েছিল। আত্মাই যদি না থাকবে তবে কেন অযথা স্বর্গ নরকের প্রসঙ্গ টানা হয়। আত্মা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করতে করতে শেষ পর্যন্ত স্পষ্টভাষী চার্বাকেরা ঈশ্বর আত্মা-পরলোক-জাতিভেদ-জন্মান্তর সবকিছুকেই নাকচ করে দেন। তারাই প্রথম বলেছিলেন বেদ অপৌরুষেয়’ নয়, এটা একদল স্বার্থান্বেষী মানুষেরই রচিত। জনমানুষের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে যাওয়া সেই সব স্বার্থান্বেষী ব্রাহ্মণদের চার্বাকেরা ভণ্ড, ধূর্ত, চোর, নিশাচর বলে অভিহিত করেছিলেন, তারা বাতিল করে দিয়েছিলেন আত্মার অস্তিত্ব, উন্মোচন করেছিলেন ধর্মের জুয়াচুরি এই বলে–
বেহেস্ত ও মোক্ষপ্রাপ্তি কি পরিত্রাণ লাভ ফাঁকা অর্থহীন অসার বুলিমাত্র, উদরযন্ত্রে বিসর্গের কারণে সবেগে উৎক্ষিপ্ত দুর্গন্ধময় ঢেকুরমাত্র। এসব প্যাক প্যাক বা। বাকচাতুরী নৈতিক অপরাধ, উন্মার্গ গমন, মানসিক ও দৈহিক ঔদার্যের ফলে পরান্নভোজী বমনপ্রবণ ব্যক্তিদের অদম্য কুৎসিত বমনমাত্র, পেটুকদের এবং উন্মার্গগামীদের বিলাস-কল্পনা। পরজগতে যাওয়ার জন্য কোনো আত্মার অস্তিত্ব নেই। বর্ণাশ্রমের নির্দিষ্ট মেকি নিয়ম-আচার আসলে কোনো ফল উৎপন্ন করে না। বর্ণাশ্রমের শেষ পরিণামের কাহিনি সাধারণ মানুষকে ঠকাবার উদ্দেশ্যে ধর্মকে গাঁজাবার থামি বিশেষ।
চার্বাকেরা বলতেন, চতুর পুরোহিতদের দাবি অনুযায়ী যদি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে বলিকৃত প্রাণী সরাসরি স্বর্গলাভ করে, তাহলে তারা নিজেদের পিতাকে এভাবে বলি দেয় না কেন? কেন তারা এভাবে তাদের পিতার স্বর্গপ্রাপ্তি নিশ্চিত করে না?
যদি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে
বলি দিলে পশু যায় স্বর্গে
তবে পিতাকে পাঠাতে স্বর্গে
ধরে বেঁধে বলি দাও যজ্ঞে।
চার্বাকেরা আরও বলতেন–
চৈতন্যরূপ আত্মার পাকযন্ত্র কোথা
তবে তো পিণ্ডদান নেহাতই বৃথা।
কিংবা
যদি শ্রাদ্ধকৰ্ম হয় মৃতের তৃপ্তের কারণ
তবে নেভা প্রদীপে দিলে তেল, উচিত জ্বলন।
আত্মা বা চৈতন্যকে চার্বাকেরা তাঁদের দর্শনে আলাদা কিছু নয় বরং দেহধর্ম বলে বর্ণনা করেছিলেন। এই ব্যাপারটা এখন আধুনিক বিজ্ঞানও সমর্থন করে। পানির সিক্ততার ব্যাপারটা চিন্তা করুন। এই সিক্ততা জিনিসটা আলাদা কিছু নয় বরং পানির অণুরই স্বভাব-ধর্ম। ‘সিক্তাত্মা’ নামে কোনো অপার্থিব সত্ত্বা কিন্তু পানির মধ্যে প্রবেশ করে তাতে সিক্ততা নামক ধর্মটির জাগরণ ঘটাচ্ছে না। বরং পানির অণুর অঙ্গসজ্জার কারণেই ‘সিক্ততা’ নামের ব্যাপারটির অভ্যুদয় ঘটেছে। চার্বাকেরা বলতেন, মানুষের চৈতন্য বা আত্মাও তাই। দেহের স্বভাব। ধর্ম হিসেবেই আত্মা বা চৈতন্যের উদ্য ঘটছে। কীভাবে এর অভ্যুদয় ঘটে? চার্বাকেরা একটি চমৎকার উপমা দিয়ে ব্যাপারটি বুঝিয়েছিলেন। বলেছিলেন, আঙ্গুর এবং মদ তৈরির অন্যান্য উপাদানগুলোতে আলাদা করে কোনো মদশক্তি নেই। কিন্তু সেই উপকরণগুলোই এক ধরনের বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো পাত্রে মিলিত করার পরে এর একটি নতুন গুণ পাওয়া যাচ্ছে, যাকে আমরা বলছি মদ। আত্মা বা চৈতন্যও তেমনই। যিশুখ্রিস্টের জন্মের প্রায় ৬০০ বছর আগের বস্তুবাদী দার্শনিকেরা এভাবেই তাদের ভাষায় রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রাণের উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করেছিলেন, কোনো রকমের আত্মার অনুকল্প ছাড়াই। তাদের এই বক্তব্যই পরবর্তীকালে ভাববাদী দার্শনিকদের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দিয়েছিল।
.
আত্মা, মন এবং অমরত্ব : বিজ্ঞানের চোখে
ভাববাদীরা যাই বলুক না কেন স্কুলের পাঠ শেষ করা ছাত্রটিও আজ জানে, মন কোনো বস্তু নয়; বরং মানুষের মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের কাজ কর্মের ফল। চোখের কাজ যেমন দেখা, কানের কাজ যেমন শ্রবণ করা, পাকস্থলীর কাজ যেমন খাদ্য হজম করা, তেমনই মস্তিষ্ক কোষের কাজ হলো চিন্তা করা। তাই নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ক্রিক তার ‘The Astonishing Hypothesis : The Scientific Search for the Soul’ গ্রন্থে পরিষ্কার করেই বলেন[২০০] ‘বিস্ময়কর অনুকল্পটি হলো : আমার ‘আমিত্ব, আমার উচ্ছাস, বেদনা, স্মৃতি, আকাঙ্ক্ষা, আমার সংবেদনশীলতা, আমার পরিচয় এবং আমার মুক্তবুদ্ধি এগুলো আসলে মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষ এবং তাদের আনুষঙ্গিক অণুগুলোর বিবিধ ব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়। মানুষ চিন্তা করতে পারে বলেই নিজের ব্যক্তিত্বকে নিজের মতো করে। সাজাতে পারে, সত্য-মিথ্যের মিশেল দিয়ে কল্পনা করতে পারে তার ভেতরে ‘মন’ বলে সত্যিই কোনো পদার্থ আছে, অথবা আছে অদৃশ্য কোনো আত্মার অশরীরী উপস্থিতি। মৃত্যুর পর দেহ বিলীন হয়। বিলীন হয় দেহাংশ, মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষ। আসলে মস্তিষ্ক স্নায়ুকোষের মৃত্যু মানেই কিন্তু ‘মন’ এর মৃত্যু, সেইসাথে মৃত্যু তথাকথিত আত্মার। অনেক সময় দেখা যায় দেহের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ঠিকমতো কর্মক্ষম আছে, কিন্তু মস্তিষ্কের কার্যকারিতা হারিয়ে গেছে। এধরনের অবস্থাকে বলে কোমা। মানুষের চেতনা তখন লুপ্ত হয়। মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা হারানোর ফলে জীবিত দেহ তখন অনেকটা জড়পদার্থের মতোই আচরণ করে। তাহলে জীবন ও মৃত্যুর যোগসূত্রটি রক্ষা করছে কে? এ কি অশরীরী আত্মা, নাকি মস্তিষ্কের স্নায়ুকোষের সঠিক কর্মক্ষমতা?
এ পর্যায়ে বিখ্যাত ক্রিকেটার রমণ লাম্বার মৃত্যুর ঘটনাটি স্মরণ করা যাক। ১৯৯৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকা স্টেডিয়ামে (বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়াম) লীগের খেলা চলাকালীন মেহেরাব হোসেন অপির একটি পুল শট ফরওয়ার্ড শর্ট লেগে ফিল্ডিংরত লাম্বার মাথায় সজোরে আঘাত করে। প্রথমে মনে হয়েছিল তেমন কিছুই হয় নি। নিজেই হেঁটে প্যাভিলিয়নে ফিরলেন; কিন্তু অল্প কিছুক্ষণ পরই জ্ঞান হারালেন তিনি। চিকিৎসকেরা তাঁকে ক্লিনিকে ভর্তি করলেন। পরদিন একুশে ফেব্রুয়ারি তাঁকে পিজি হাসপাতালের নিউরোসার্জারি বিভাগে ভর্তি করা হলো সেখানে তার অপারেশন হলো, কিন্তু অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকেই যাচ্ছিল। পরদিন বাইশে ফেব্রুয়ারি ডাক্তাররা ঘোষণা করলেন যে, মস্তিষ্ক তার কার্যকারিতা হারিযেছে। হার্ট-লাং মেশিনের সাহায্যে কৃত্রিমভাবে হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুসের কাজ চলছিল।
২৩ ফেব্রুয়ারি বিকেল সাড়ে তিনটায় তার আইরিশ স্ত্রী কিমের উপস্থিতিতে হার্ট লাং মেশিন বন্ধ করে দিলেন চিকিৎসকেরা থেমে গেল লাম্বার হৃৎস্পন্দন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে-ডেথ সার্টিফিকেটে মৃত্যুর তারিখ কোনটি হওয়া উচিত? ২২ নাকি ২৩ ফেব্রুয়ারি? আর তার মৃত্যুক্ষণটি নির্ধারণ করলেন কারা? আজরাইল/যমদুত নাকি চিকিৎসারত ডাক্তারেরা?
এ ব্যাপারটি আরও ভালোভাবে বুঝতে হলে মৃত্যু নিয়ে দু’চার কথা বলতেই হবে। জীবনের অনিবর্তনীয় পরিসমাপ্তিকে (Irreversible Cessation of Life) বলে মৃত্যু। কেন জীবের মৃত্যু হয়? কারণ মৃত্যুবরণের মাধ্যমে আমাদের জীবন তাপগতীয় স্থিতাবস্থা (Thermodynamic Equilibrium) প্রাপ্ত হয়। তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র মানতে গেলে জীবনের উদ্দেশ্য আর কিছুই নয় নিবিষ্টচিত্তে এন্ট্রপি বাড়িয়ে চলা। আমাদের খাওয়া দাওয়া, শয়ন, ভ্রমণ, মৈথুন, কিংবা রবিঠাকুরের কবিতা পাঠের আনন্দ সবকিছুর পেছনেই থাকে মোটাদাগে কেবল একটি মাত্র উদ্দেশ্য ফেইথফুলি এনট্রপি বাড়ানো। সেটা আমরা বুঝতে পারি আর নাই পারি! জন্মের পর থেকে সারা জীবন ধরে আমরা এনট্রপি বাড়িযে বাড়িযে প্রকৃতিতে তাপগতীয় অসাম্য তৈরি করি, আর শেষমেশ পঞ্চত্ব প্রাপ্তির মাধ্যমে অন্যান্য জড় পদার্থের মতো নিজেদের দেহকে তাপগতীয় স্থিতাবস্থায় নিয়ে আসি। কিন্তু কীভাবে এই স্থিতাবস্থার নির্দেশ আমরা বংশপরম্পরায় বহন করি? জীববিজ্ঞানের চোখে দেখলে, আমরা (উদ্ভিদ এবং প্রাণী) উত্তরাধিকার সূত্রে বিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের পূর্বপুরুষদের যারা যৌনসংযোগের মাধ্যমে বংশবিস্তার করে প্রকৃতিতে টিকে রয়েছে তাদের থেকে মরণ জিন (Death Gene) প্রাপ্ত হয়েছি এবং বহন করে চলেছি। এই ধরনের জিন (মরণ জিন) তার পরিকল্পিত উপায়েই মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে চলেছে। যৌনজননের মাধ্যমে বংশবিস্তারের ব্যাপারটিতে আমরা এখানে গুরুত্ব দিচ্ছি। কারণ, যে সমস্ত প্রজাতি যৌনজননকে বংশবিস্তারের একটি মাধ্যম হিসেবে বেছে নিয়েছে, তাদের মৃত্যু নামক ব্যাপারটিকেও তার জীবজগত বৈশিষ্ট্য হিসেবে গ্রহণ করে নিতে হয়েছে। দেখা গেছে স্তন্যপায়ী জীবের ক্ষেত্রে সেক্স-সেল বা যৌন কোষগুলোই (জীববিজ্ঞানীরা বলেন ‘জার্মপ্লাজম’) হচ্ছে একমাত্র কোষ যারা সরাসরি এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে নিজেদের জিন সঞ্চারিত করে টিকে থাকে। জীবনের এই অংশটি অমর। কিন্তু সে তুলনায় সোমাটিক সেল দিয়ে তৈরি দেহকোষগুলো হয় স্বল্পায়ুর। অনেকে এই ব্যাপারটির নামকরণ করেছেন প্রোগ্রামড ডেথ’। এ যেন অনেকটা বেহুলা-লখিন্দর কিংবা বাবর-হুঁমায়ুনের মতো ব্যাপার: জননকোষের অমরত্বকে পূর্ণতা দিতে গিয়ে দেহকোষকে বরণ করে নিতে হয়েছে মৃত্যু-ভাগ্য। প্রখ্যাত জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স হালকা চালে তার ‘সেলফিশ জিন’ বইয়ে বলেছেন, মৃত্যু’ও বোধহয় সিফিলিস বা গনোরিয়ার মতো এক ধরনের সেজুলি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ’ যা আমরা বংশপরম্পরায় সূচনালগ্ন থেকে বহন করে চলেছি! ভাইরাস ব্যাকটেরিয়ার মতো সরলকোষী জীব যারা যৌনজনন নয়, বরং কোষ বিভাজনের মাধ্যমে প্রকৃতিতে টিকে আছে তারা কিন্তু আক্ষরিক অর্থেই অমর। এদের দেহ কোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে বিভাজিত হয়, তার পর বিভাজিত অংশগুলোও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে পুনরায় বিভাজিত হয়; কোনো অংশই আসলে সেভাবে মৃত্যুবরণ করে না।
ছবি। পেজ ২০৯
চিত্র : (উপরে) স্বামীর সাথে হেনরিযেটা ল্যাকস, ১৯৪৫ সালে তোলা ছবি এবং (নিচে) ল্যাবরেটরিতে ‘অমর’ হেলা কোষ।
আবার অধিকাংশ ক্যান্সার কোষই অমর, অন্তত তাত্বিকভাবে তো বটেই। একটি সাধারণ কোষকে জীবদ্দশায় মোটামুটি গোটা পঞ্চাশেক বার কালচার বা পুনরুৎপাদন করা যায়। এই সীমাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে হেফ্লিক লিমিট (Hayflick Limit)। কখনও সখনো ক্যান্সারাক্রান্ত কোনো কোনো কোষে সংকীর্ণ টেলোমার থাকার কারণে এটি কোষস্থিত ডিএনএ’র মরণ জিনকে স্থায়ীভাবে ‘সুইচ অফ করিয়ে দেয়। এর ফলে এই কোষ তার আভ্যন্তরীণ ‘হেফ্লিক’ লিমিটকে অতিক্রম করে যায়। তখন আক্ষরিকভাবেই অসংখ্যবার মানে অসীমসংখ্যক বার সেই কোষকে কালচার করা সম্ভব। এই ব্যাপারটাই তাত্ত্বিকভাবে কোষটিকে প্রদান করে অমরত্ব। হেনরিযেটা ল্যাকস নামে এক মহিলা ১৯৫২ সালে সার্ভিকাল ক্যান্সারে মারা যাওয়ার পর ডাক্তাররা ক্যান্সারাক্রান্ত দেহকোষটিকে সরিয়ে নিয়ে ল্যাবে রেখে দিয়েছিল। এই কোষের মরণ জিন স্থায়ীভাবে ‘সুইচ অফ করা এবং কোষটি এখনও ল্যাবরেটরির জারে ঠিকঠাক ভাবে ‘জীবিত অবস্থায় আছে। প্রতিদিনই এই সেল থেকে কয়েকশ বার করে সেল-কালচার করা হচ্ছে, এই কোষকে এখন ‘হেলা কোষ’ নামে অভিহিত করা হয়। যদি কোনোদিন ভবিষ্যৎ-প্রযুক্তি আর জৈবমূল্যবোধ (Bioethics) আমাদের সেই সুযোগ দেয়, তবে আমরা হয়ত হেলাকোষ ক্লোন করে হেনরিযেটাকে আবার আমাদের পৃথিবীতে ফেরত আনতে পারব। সম্প্রতি সাংবাদিক রেবেকা স্কলুট হেনরিযেটা ল্যাকস এবং তার এই ‘অমরত্বের জীবন নিয়ে একটি চমৎকার বই লিখেছেন ‘দ্য ইমমরটাল লাইফ অব হেনরিযেটা ল্যাকস’ নামে[২০১]।
আবার ব্রাইন শ্রিম্প (brine shrimp), গোলকৃমি বা নেমাটোড, কিংবা টার্ডিগ্রেডের মতো কিছু প্রাণী আছে যারা মৃত্যুকে লুকিয়ে রাখতে পারে, জীববিজ্ঞানের ভাষায় এ অবস্থাকে বলে ‘ক্রিপ্টোবায়োটিক স্টেট। যেমন, ব্রাইন শ্রিম্পগুলো লবণাক্ত পানিতে সমানে বংশবৃদ্ধি করতে থাকে, কিন্তু পানি যখন শুকিয়ে যায়, তখন তারা ডিম্বাণু উৎপাদন, এমনকি নিজেদের দেহের বৃদ্ধি কিংবা মেটাবোলিজম পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়। শ্রিম্পগুলোকে দেখতে তখন মৃত মনে হলেও এরা আসলে মৃত নয় বরং এদের এই মরণাপন্ন অবস্থার মধ্যেও জীবনের বীজ লুকানো থাকে। এই অবস্থাটিকেই বলে ‘ক্রিপ্টোবায়োটিক স্টেট’। কখনও তারা পানি খুঁজে পেলে আবারও নতুন করে ‘নবজীবনপ্রাপ্ত হয়। এদের অদ্ভুতুড়ে ব্যাপারগুলো অনেকটা ভাইরাসের মতো ভাইরাসের কথা আরেকবার চিন্তা করা যাক। ভাইরাস জীবন ও জডের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থান করে। ভাইরাসকে কেউ ড বলতে পারেন, আবার জীবিত বলতেও বাধা নেই। এমনিতে ভাইরাস ‘মৃতবৎ’, তবে তারা বেঁচে ওঠে অন্য জীবিত কোষকে আশ্রয় করে। ভাইরাসে থাকে প্রোটিনবাহী নিউক্লিযিক এসিড। এই নিউক্লিযিক এসিডই ভাইরাসের যাবতীয় বৈশিষ্ট্যের আধার। উপযুক্ত পোষক দেহ পাওয়ার আগ পর্যন্ত তারা ক্রিপ্টোবায়োটিক স্টেট’-এ জীবনকে লুকিয়ে রাখে। আর তারপর উপযুক্ত দেহ পেলে আবারও কোষ বিভাজনের মাধ্যমে অমরত্বের খেলা চালিয়ে যেতে থাকে।
কাজেই দেখা যাচ্ছে ‘মৃত্যু’ ব্যাপারটি সব জীবের জন্যই অত্যাবশ্যকীয় নিয়ামক নয়। ভাইরাসের আণবিক সজ্জার মধ্যেই আসলে লুকিয়ে আছে অমরত্বের বীজ। এই অঙ্গসজ্জাই আসলে ডিএনএ-র মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেয় তারা কখন ঘাপটি মেরে ‘ক্রিপ্টোবায়োটিক স্টেট’-এ পড়ে থাকবে, আর কথন নবজীবনের ঝরনাধারায় নিজেদের আলোকিত করবে। সে হিসেবে ভাইরাসেরা আক্ষরিক অর্থেই কিন্তু অমর—এরা স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে না। তবে মানুষের নিজের প্রয়োজনে রাসায়নিক জীবাণুনাশক ঔষধপত্রাদির উদ্ভাবন ও তার প্রযোগে জীবাণনাশের ব্যাপারটি এক্ষেত্রে আলাদা। ঔষধের প্রযোগে আসলে এদের অঙ্গসজ্জা ভেঙে দেওয়া হয়, যেন তারা আবার পুনর্জীবন প্রাপ্ত হয়ে রোগ ছড়াতে না পারে। ঠিক একই রকমভাবে অত্যধিক বিকিরণ শক্তি প্রয়োগ করেও ভাইরাসের এই দেহগত অঙ্গসজ্জা ভেঙে দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে এদের আণবিক গঠন বিনষ্ট হবে এবং এদের জীবনের সুপ্ত আধার হারিয়ে যাবে। ফলে উপযুক্ত পরিবেশ পেলেও এরা আর পুনর্জীবন প্রাপ্ত হবে না। যারা জীবন-মৃত্যুর ব্যাপারটিকে আরও ভালোমতো বিজ্ঞানের গভীরে গিয়ে বুঝতে চান তারা আণবিক জীববিজ্ঞানী উইলিয়াম সি ক্লার্কের লেখা ‘সেক্স অ্যান্ড দি অরিজিন অফ ডেথ[২০২] বইটি পড়তে পারেন। ‘মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে (অবসর প্রকাশনা, ২০০৭) বইটির প্রথম অধ্যায়েও বেশ কিছু আকর্ষণীয় উদাহরণ হাজির করে জীবন-মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। উৎসাহী পাঠকেরা পড়ে নিতে পারেন।
রমন লাম্বার মতো মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয়েছে দলছুট ব্যান্ডের গায়ক সঞ্জীব চৌধুরীরও এই সুপ্রতিষ্ঠিত গায়কের ক্ষেত্রেও রক্তক্ষরণে মস্তিষ্ক তার কার্যক্ষমতা। হারিয়েছিল। তিনি চলে গিয়েছিলেন কোমায়। কোমায় একবার কেউ চলে গেলে তাকে পুনরায় জীবনে ফেরত আনা অনেক ক্ষেত্রেই অসম্ভব ব্যাপার। কোমার স্থায়িত্ব সাধারণত দুই থেকে চার সপ্তাহ থাকে। যারা চেতনা ফিরে পান, তারা সাধারণত ২/১ দিনের মধ্যেই তা ফিরে পান। বাকিদের অনেকেই মারা যান, কিন্তু অনেকে কোমা থেকে উঠে আসেন বটে, কিন্তু রয়ে যান অচেতন দশায় যাকে মেডিক্যালের ভাষায় বলে ‘নিষ্ক্রিয় দশা’ বা ‘ভেজিটেটিভ স্টেট’ (Vegetative state)। ডাক্তার এবং রোগীর আত্মীয়স্বজনদের জন্য এ এক অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। কারণ রোগীর দেহটা বেঁচে থাকলেও মস্তিষ্ক থাকে নিষ্ক্রিয়। টেকনিক্যালি, এদের তথন মৃতও বলা যায় না, কারণ শ্বাস-প্রশ্বাসসহ কিছু শারীরিক কাজ-কর্ম চলতে থাকে স্বাভাবিকভাবেই। মাসাধিককাল পর এধরনের রোগীরা পৌঁছে যান স্থায়ী নিষ্ক্রিয় দশা’য় (Persistent Vegetative State)। যতই দিন পেরুতে থাকে রোগীর সচেতনতা আবারও ফিরে আসার সম্ভাবনা কমতে থাকে। অক্সিজেনের অভাবে মস্তিষ্কের কোষগুলো ধীরে ধীরে মারা যেতে থাকে। ওই সময় কৃত্রিমভাবে তার দেহকে বাঁচিয়ে রাখা গেলেও তার চৈতন্য আর ফেরত আসে না। ১৯৯৪ সালে আমেরিকার মাল্টি সোসাইটি টাস্কফোর্সের এগারো জন গবেষকের একটি গবেষণা থেকে জানা যায়, স্থায়ী নিষ্ক্রিয় দশায় রোগী একবার পৌঁছে গেলে আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা চলে যায় শূন্যের কাছাকাছি[২০৩]। দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পর ডাক্তারদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হয় রোগীর জীবন-প্রদীপ নির্বাপণ করার, কারণ ততদিনে তাদের জানা হয়ে যায় যে, এ রোগী আর চৈতন্য ফিরে পাবে না। পাঠকদের নিশ্চয় ফ্লোরিডার টেরি শাইভোর ঘটনার কথা মনে আছে, যার খবর সারা আমেরিকায় আলোড়ন তুলেছিল। ১৫ বছর ধরে স্থায়ী নিষ্ক্রিয় দশা’য় থাকার পর টেরি শাইভোর স্বামীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০০৫ সালে যখন ডাক্তাররা টেরির মুখ থেকে খাদ্যনালী খুলে দিয়ে তার ‘দেহাবসান ঘটানোর উদ্যোগ নিলেন, তখন তা আমেরিকার রাজনৈতিক মহলকে তোলপাড় করে তুলেছিল। রক্ষণশীলেরা ডাক্তারদের এ নাফরমানিকে দেখেছিলেন খোদার ওপর খোদকারি’র দৃষ্টান্ত হিসেবে। কিন্তু ডাক্তারদের করণীয় ছিল না কিছুই। টেরি শাইভোর সিটি স্ক্যান এবং এমআরআই থেকে দেখা গিযেছিল অক্সিজেনের অভাবে ব্রেন টিস্যুর অনেকটুকুই নষ্ট হয়ে গেছে। আদালতের রায়ও গিয়েছিল ডাক্তারদের অনুকুলেই।
এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, ডাক্তারেরা কোন আলামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেন যে, রোগী স্থায়ীভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে গেছে নাকি চেতনা ফিরে পাওয়ার আশা আছে? এটি নিঃসন্দেহ, ডাক্তার যদি বোঝেন যে, চেতনা ফিরে আসার সম্ভাবনা কিছুটা হলেও আছে, তাহলে কখনোই দেহাবসানের মাধ্যমে রোগীর মৃত্যু ত্বরান্বিত করবেন না। ডাক্তাররা আসলে সিদ্ধান্ত নেন ‘ব্রেন ইমেজিং টেকনিক নামে এক আধুনিক পদ্ধতির সাহায্যে মস্তিষ্ক পর্যবেক্ষণ করে। তারা দেখেন আহত মস্তিষ্কে আদৌ কোনো ধরনের বোধ শক্তি কিংবা চেতনার আলামত পাওয়া যাচ্ছে কিনা। অনেক সময় এই আলামত খুব সুপ্ত অবস্থায় থাকে, যা সহজে ধরা যায় না। এই অবস্থাকে বলা যেতে পারে, ন্যূনতম সচেতন অবস্থা বা মিনিমালি কনশাস। স্টেট। কাজেই ডাক্তারদেরকে খুব যত্ন নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয়, এবং তা দীর্ঘমেয়াদী। যেমন, এড্রিয়ান ওযেনের নেতৃত্বে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষকের তত্ত্বাবধানে ২৩ বছরের এক তরুণী। চিকিৎসারত অবস্থায় আছে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় আক্রান্ত এ তরুণীর মস্তিষ্ক বেশ ভালোভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এক সপ্তাহ কোমায় থাকার পর চড়াই উৎরাই পেরিয়ে ‘নিষ্ক্রিয় দশা’য় এসে পৌঁছেন। সেই তরুণী এখন চোখের পাপড়ি মেলতে পারেন, কিন্তু বাইরের কোনো নির্দেশ পালন করার ন্যূনতম আলামত কখনোই দেখান নি। ডাক্তারেরা মেয়েটির মস্তিষ্ক কী অবস্থায় আছে তা নিঃসন্দেহ হওয়ার জন্য বিভিন্ন পরীক্ষা চালালেন। যেমন, রোগীর সামনে গিয়ে বললেন, ‘কফির জন্য চিনি আর দুধ টেবিলে রাখা আছে, খাও’ এই মন্তব্যের কী প্রতিক্রিয়া রোগীর মাথায় পাওয়া যায় তা জানার জন্য MRI স্ক্যান করে খুঁজে দেখলেন চিকিৎসকেরা। দেখলেন, মস্তিষ্কের ভেতরে টেম্পোলার গাইরি নামের যে জায়গাটা আছে সেটা উদ্দীপ্ত হচ্ছে। মাথার এই জায়গাটা সুস্থ মানুষদের ক্ষেত্রে কথাবার্তা শোনা এবং বোঝার কাজে ব্যবহৃত হয়। কাজেই এটুকু বোঝা গেল, হয়ত মেয়েটি সচেতন। কিন্তু চিকিৎসকেরা নিশ্চিত হতে পারলেন না। কারণ অনেক সময় গভীর ঘুমে থাকা মানুষের সামনেও এধরনের নির্দেশ দিলে তাদের মাথার এই জায়গাগুলো উদ্দীপ্ত হয়।
আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্য ডাক্তারেরা ঠিক করলেন, রোগীকে দিয়ে টেনিস খেলাবেন। রোগীকে নির্দেশ দেওয়া হলো মনে করো তুমি টেনিস গ্রাউন্ডে আছ। আসো এবার আমার সাথে টেনিস খেল দেখি! নিঃসন্দেহে টেনিস খেলার প্রক্রিয়াটি এমনিতে বেশ জটিল। মাথার অনেকগুলো অংশের সমন্বিত সংযোগ করে তবে খেলাটা ঠিকমতো খেলতে হয়। মাথার একটি অংশ আছে ‘সাপ্লিমেন্টারি মোটর’ এলাকা। এই এলাকাটা দেহের হাত-পাসহ অন্যান্য অঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। দেখা গেল তরুণীর মোটর এলাকা অনবরত উদ্দীপ্ত হচ্ছে। টেনিস খেললে তাই হওয়ার কথা। আবার রোগীকে নির্দেশ দেওয়া হলো এবার মনে করো তুমি তোমার বাড়িতে এক ঘর থেকে আরেক ঘরে যাচ্ছ’ মস্তিষ্ক স্ক্যান করে দেখা গেল এবারে মাথার ‘প্রিমোটর, প্যারিটাল আর প্যারাহিপোক্যাম্পাল’এলাকা উদ্দীপ্ত হচ্ছে। একজন সুস্থ মানুষের ক্ষেত্রেও তাই হয়। বোঝা গেল মেয়েটি সম্ভবত সচেতন অবস্থায় রয়েছে। ডাক্তারেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এধরনের রোগীর আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা একেবারে শূন্য নয়, বরং পাঁচ ভাগের এক ভাগ। মন্দ নয় সম্ভাবনা। আর সেজন্যই মেয়েটিকে কৃত্রিম উপায়ে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, এবং মেয়েটিও এভাবেই ‘মিনিমালি কনশাস স্টেটে রয়েছে কখনও ডাক্তারের নির্দেশ মানছে, কখনও নয়।
অনেকদিন ধরে ‘মিনিমালি কনশাস স্টেটে’ থাকার পর আবার মোটামুটি সচেতন অবস্থায় ফিরার উদাহরণ হচ্ছে আরকান্সাসের টেরি ওয়ালিসের ঘটনা। তিনিও এক ভয়ংকর ধরনের সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ১৯৮৪ সালে চেতনা হারান এবং প্রায় ১৯ বছর ধরে ন্যূনতম সচেতন অবস্থা বা ‘মিনিমালি কনশাস স্টেট’-এ ছিলেন। দীর্ঘদিন পর ২০০৩ সালে এসে টেরি ওয়ালিস কথা বলতে শুরু করেন। সেইসাথে হাত-পা নাড়ানোর ক্ষমতাও কিছুটা ফিরে পান। এখনও তিনি হাঁটতে চলতে পারেন না, এবং কারো না কারো সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে তাকে থাকতে হয়, কিন্তু তারপরও টেরি ওয়ালিসের উন্নতি লক্ষণীয়। এ থেকে বোঝা যায়, ন্যূনতম সচেতন অবস্থা বা মিনিমালি কনশাস স্টেট থেকে আবার সচেতনতায় প্রত্যাবর্তন সম্ভব; কিন্তু স্থায়ী নিষ্ক্রিয় দশা’ বা পার্মানেন্ট ভেজিটেটিভ স্টেট থেকে প্রত্যাবর্তন অনেকটা দুরাশাই বলতে হবে। নিচের ছবিটি দেখলে এ ব্যাপারটি হয়ত পাঠকদের জন্য আরও পরিষ্কার হবে–
ছবি। পেজ ২১৭
চিত্র : মস্তিষ্কে আঘাত পেয়ে কোমায় চলে যাওয়া রোগীদের বিভিন্ন অবস্থা।
মৃত্যু নিয়ে আরও কিছু কথা বলা যাক। আসলে মানুষের মতো বহুকোষী উচ্চশ্রেণির প্রাণীদের মৃত্যু দুই ধরনের। দেহের মৃত্যু (Clincal Death) এবং কোষীয় মৃত্যু (Cellular Death)। দেহের মৃত্যুর স্বল্প সময় পরেই কোষের মৃত্যু ঘটে। মানব দেহের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ রয়েছে মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড, আর ফুসফুস। যেকোনো একটির বা সবগুলোর কার্যকারিতা নষ্ট হলে মৃত্যু হতে পারে। যেমন, মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বন্ধ হলে কোমা হয়, রমণ লাম্বা কিংবা সঞ্জীব চৌধুরীর ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটেছে; হৃৎপিণ্ডের কার্যকারিতা বন্ধ হওয়াকে বলে সিনকোপ, আর ফুসফুসের কার্যকারিতা বন্ধ হওয়াকে বলে আসফিক্সি। ত্রিশ চল্লিশ বছর আগেও কিন্তু মৃত্যু ব্যাপারটার সংজ্ঞা দেওয়া এতটা কঠিন ছিল না। খুব সহজ সংজ্ঞা। হৃৎস্পন্দন থেমে যাওয়ার সাথে সাথেই কিংবা ফুসফুস তার হাপরের উঠানামা বন্ধ করে দেওয়ার সাথে সাথেই ব্যক্তির জীবন-প্রদীপ নির্বাপিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হতো। কিন্তু ১৯৬৮ সালে হৃৎসংস্থাপন (Heart Transplant) প্রক্রিয়ার আবিষ্কার এবং এ সংক্রান্ত প্রযুক্তির উন্নয়নের পর মৃত্যুর এই সংজ্ঞা কিন্তু বদলে যায়। কীভাবে এখন হলফ করে সেই ‘হৃদদাতা’কে মৃত বলা যাবে যখন চোখের সামনেই তার হৃদয় অন্যের দেহে স্পন্দিত হয়ে চলেছে? চিকিৎসা বিজ্ঞান পুরো ব্যাপারটিকে আরও জটিল করে ফেলোে শ্বাসযন্ত্র বা রেস্পিরেটর আবিষ্কার করে-যেটি হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুসকে কৃত্রিমভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। উত্তরাধুনিক কোনো কবি কিন্তু এখন মৃত্যু নিয়ে কবিতা লিখতেই পারেন এই বলে যে ‘হে হিমশীতল মৃত্যু তুমি হচ্ছে রেস্পিরেটর সুইচের সহসা নির্বাপণ!
যত দিন যাচ্ছে ততই কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে জীবন আয়ু ত্বরান্বিত করার ব্যাপারটি খুব সাধারণ একটি বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কল্যাণে অনেক মৃত্যুপথযাত্রী অসুস্থ রোগীর মৃত্যু নানাভাবে বিলম্বিত করা গেছে কারো কারো ব্যাপারে কম সময়ের জন্য, আবার কারো ব্যাপারে দীর্ঘ সময়ের জন্য। যেমন ধরুন বার্নি ক্লার্ক নামের এক ডেনটিস্ট ভদ্রলোকের উদাহরণ, যিনি ১৯৮২ সালে নিজের রোগাক্রান্ত হৃৎপিণ্ডের পরিবর্তে একটি যান্ত্রিক হৃদয় নিয়ে বেঁচে ছিলেন কয়েক মাস যাবত। আবার ১৯৮৪ সালে সদ্য জন্মলাভ করা শিশু কে কে অতিরিক্ত ২০দিন বাঁচিয়ে রাখা গিয়েছিল একটি বেবুনের হৃৎপিণ্ড সংযোজন করে।
আশির দশকের প্রথম দিকে জেমি ফিস্কের ‘জীবন প্রাপ্তির উদাহরণটি আরেকটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ হিসেবে উঠে আসতে পারে পাঠকদের কাছে। এগারো মাসের শিশু জেমি আর হয়ত বড়জোর একটা ঘণ্টা বেঁচে থাকতে পারত-তার জন্মগত ত্রুটিপূর্ণ যকৃৎ নিয়ে। তার বাঁচার একটিমাত্র ক্ষীণ সম্ভাবনা নির্ভর করছিল যদি কোনো সুস্থ শিশুর যকৃৎ কোথাও পাওয়া যায় আর ওটি ঠিকমতো জেমির দেহে সংস্থাপন করা সম্ভব হয়ে ওঠে। কিন্তু এত ছোট বাচ্চার জন্য কোথাওই কোনো যকৃত পাওয়া যাচ্ছিল না। যে সময়টাতে জেমি ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছিল আর ঠিক সেসময়টাতেই হাজার মাইল দূরে একটি ছোট্ট শহরে এক বিচ্ছিরি ধরনের সড়ক দুর্ঘটনায় পড়া দশ মাসের শিশু জেসি বেল্লোনকে তাড়াহুড়ো করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল হাসপাতালে। যদিও মাথায় তীব্র আঘাতের ফলে জেসির মস্তিষ্ক আর কাজ করছিল না, কিন্তু দেহের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে কিন্তু রেস্পিরেটরের সাহায্যে ঠিকই কর্মক্ষম করে রাখা হয়েছিল। জেসির বাবা রেডিওতে দিন কয়েক আগেই একটি যকৃতের জন্য জেমির অভিভাবকদের আর্তির কথা শুনেছিলেন। শোকগ্রস্ত পিতা। এত দুঃথের মাঝেও মানবিক কর্তব্য বোধকে অস্বীকার করেন নি। তিনি পার্মানেন্ট ভেজিটেশনে চলে যাওয়া নিজের মেয়ের অক্ষত যকৃৎটি জেমিকে দান করে তাকে বাঁচানোর চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। জেসির রেস্পিরেটর বন্ধ করে দিয়ে তার যকৃৎ সংরক্ষিত করে মিনেসোটায় পাঠানোর ব্যবস্থা করা হলো। জেমির বহু প্রতীক্ষিত অস্ত্রোপচার সফল হলো। এভাবেই জেসির আকস্মিক মৃত্যু সেদিন জেমি ফিস্ককে দান করল যেন এক নতুন জীবন। সেই ধার করা যকৃৎ নিয়ে পুনর্জীবিত জেমি আজও বেঁচে আছে-পড়াশোনা করছে, দিব্যি হেসে খেলে বেড়িয়ে পার করে দিয়েছে জীবনের পঁচিশটি বছর!
এবার আসুন প্রিয় পাঠক আপনাদের জিমি টন্টলিউজের ঘটনাটির সাথে পরিচয় করিয়ে দেই। এক শুভ্র সকালে তরুণ জিমি লেক মিশিগানের ওপর স্কেট করতে গিয়ে একস্তর পুরু বরফের আস্তরণ ভেদ করে শীতল জলে তলিয়ে যায়। ও অবস্থাতেই ছিল সে অনেকক্ষণ প্রায় আধাঘণ্টা পরে পথচারীরা তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে। দেখে মনে হচ্ছিল জিমি মারাই গিযেছে বুঝি, তার হৃৎস্পন্দন, নাডি, শ্বাসপ্রশ্বাস কিছুই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে গিয়ে সেবাশুশ্রূষা শুরু করার প্রায় এক ঘণ্টা পরে ছেলেটির দেহে যেন জীবনের বৈশিষ্ট্য আবারও ‘নতুন করে ফিরে আসতে শুরু করল। আসলে ঠাণ্ডা পানির তীব্র ঝাঁপটা জিমির দেহকে একেবারে অসাড় করে দিয়েছিল। যদিও সাময়িক সময়ের জন্য হৃৎস্পন্দন এবং ফুসফুসও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তার অন্যান্য প্রয়োজনীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো কিন্তু একটি মিনিমাম লেভেলে কাজ করে যাচ্ছিল। ঘটনাক্রমে সেই শক্তিটুকুই জিমির দেহে পুনরায় হৃৎস্পন্দন আর শ্বাসপ্রশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্য ছিল যথেষ্ট। চিকিৎসকেরা একমত যে, বরফ শীতল পানি অনেক ক্ষেত্রেই ক্লোরোফর্মের মতো অবচেতকের কাজ করে অতিশীতল তাপমাত্রায় তখন দেহ চলে যায় ‘হাইবারনেশন’ বা শীতনিদ্রা-ব্যাঙ, সাপ, বাদুড়, কিছু মাছের মধ্যে যা হরহামেশাই ঘটতে দেখা যায়। দেখা গেছে এধরনের অবস্থায় দেহের বিপাকক্র্যির হার কমে যায়, এবং দেহের জন্য যতটুকু খাবার কিংবা অক্সিজেন সুস্থ অবস্থায় প্রয়োজন, তার চেয়ে অনেক কম শক্তি খরচ করে দেহকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। আর তাই এধরনের পরিস্থিতিতে দীর্ঘক্ষণ কাটিযেও বেঁচে যাওয়ার উদাহরণ কিন্তু জিমি একা নয়। লাস ভেগাসের মুরে ব্রাউন আধাঘণ্টা, ইউটাহ শহরে মিশেল ফাফ এক ঘণ্টা আর কানাডার তেরো মাসের শিশু এরিকা নরডবাই দুই ঘণ্টা ধরে বরফ-জলে ডুবে অচেতন হয়ে থাকবার পরও চিকিৎসকরা তাদের কিন্তু বাঁচাতে পেরেছেন। তবে সবচেয়ে অবাক করেছে জাপানের মিৎসুতাকা উছিকোশির ঘটনা। জাপানের রোকো পাহাড়ের তুষারাচ্ছন্ন পরিবেশে ২৪ দিন ধরে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকার পরও কোব্ব সিটি জেনারেল হাসপাতালে নেওয়ার পর তাকে শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়ে তোলা গেছে[২০৪]
এবারে আসি মৃত্যু ক্ষণের আলোচনায়। রোগীর মৃত্যুর সঠিক সময় নির্ধারণ করাটাও অনেকক্ষেত্রে অসুবিধাজনক, কারণ দেখা গেছে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেহের মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকে, যেমন মস্তিষ্ক ৫ মিনিট, হৃৎপিণ্ড ১৫ মিনিট, কিডনি ৩০ মিনিট, কঙ্কাল পেশি ৬ ঘণ্টা। অঙ্গ বেঁচে থাকার অর্থ হলো তার কোষগুলো বেঁচে থাকা। কোষ বেঁচে থাকে ততক্ষণই যতক্ষণ এর মধ্যে শক্তির জোগান থাকে। শক্তি উৎপন্ন হয় কোষের অভ্যন্তরস্থ মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে। মাইটোকন্ড্রিয়ার কার্যকারিতা ক্ষুণ্ণ হলে কোষেরও মৃত্যু হয়। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, মৃত্যু কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং একটি প্রক্রিয়া। দেহের মৃত্যু দিয়ে এর প্রক্রিয়া শুরু হয়, শরীরের শেষ কোষটির মৃত্যু পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে।
.
আত্মা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা
আত্মার ব্যাপারটা এতই কৌতূহলোদ্দীপক যে, সত্যিই দেহাতীত কোনো অস্তিত্ব আছে কিনা তা অনেকেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যাচাই করে দেখতে চেয়েছেন। আর আত্মায় বিশ্বাসী গবেষকেরা আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার আয়োজন করেছেন। ১৯২১ সালে ড. ডানকান ম্যাকডোগাল তার বিখ্যাত ২১ গ্রাম পরীক্ষা সম্পন্ন করেন। তিনি দাবি করেন, এই পরীক্ষার মাধ্যমে তিনি আত্মার ওজন নির্ণয় করতে পেরেছেন। তার পরীক্ষা ছিল খুবই সহজ। তার দাবি অনু্যায়ী তিনি ছয় জন রোগীর মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলেন এবং মৃত্যুর ঠিক আগের এবং পরবর্তী মুহূর্তের দেহের ওজন মেপে দেখেন, ওজনের পার্থক্য ১১ গ্রাম থেকে ৪৩ গ্রামের মধ্যে (মিডিয়ায় যেমন আত্মার ওজন একদম মাপমতো ২১ গ্রাম বলে প্রচার করা হয়, হুবহু তা অবশ্য পান নি।) ঠিক একইভাবে তিনি ছয়টি কুকুরের মৃত্যু পর্যবেক্ষণ করেন, এবং একইভাবে ওজন মেপে দেখেন ওজনের কোনো পার্থক্য পাওয়া যাচ্ছে না। এ থেকে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন, মানুষেরই কেবল আত্মা আছে। কুকুর বিড়াল জাতীয় ইতর প্রাণীর আত্মা নেই। তার এই পরীক্ষা মিডিয়ায় চমক সৃষ্টি করলেও বৈজ্ঞানিক মহলে অচিরেই পরিত্যক্ত হয়। কারণ ম্যাকডোগাল নিজে বা অন্য কেউই এই ২১ গ্রামের পরীক্ষা পুনর্বার সম্পন্ন করে সত্যাসত্য নির্ণয় করতে পারেন নি, যা বৈজ্ঞানিক মহলে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার অন্যতম মাপকাঠি। শুধু পরীক্ষাটি পুনর্বার সম্পন্ন করা গেল না-এটিই কেবল নয়, পরীক্ষার উপাত্ত বা ডেটা নিয়েও ছিল সমস্যা। ম্যাকডোগাল নিজেই গবেষণাপত্রে স্বীকার করেছিলেন, তার গৃহীত ছয়টি উপাত্তের মধ্যে দুটোকে নিজেই বাতিল করে দিয়েছিলেন কোনো ‘ভ্যালু না থাকার কারণে। দুটো উপাত্তে দেখালেন যে ওটাতে ওজন ‘ড্রপ করেছে, এবং পরবর্তীকালে এই ওজন আরও কমে গেল (আত্মা বোধহ্য ‘খ্যাপে থ্যাপে’ দেহত্যাগ করছিল!), আরেকটি ডেটায় ওজন হ্রাস না ঘটে বরং বিপরীতটাই ঘটতে দেখা গিয়েছিল, পরে এর সাথে যুক্ত হয়েছিল অন্য কোনো হ্রাসের ব্যাপার-স্যাপার (এক্ষেত্রে বোধহয় আত্মা সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না উনি কি দেহত্যাগ করবেন, নাকি করবেন না, নাকি দেহত্যাগ করে আবারও দেহে পুনঃ প্রবেশ করবেন, নাকি দেহকে চিরবিদায় জানাবেন!); শুধু একটি উপাত্ত থেকে ওজন হ্রাসের ব্যাপারটা আঁচ করা গেল এবং জানা গেল এটি এক আউন্সের ৩/৪ ভাগ[২০৫]। এই একটিমাত্র ডেটা থেকে আসা সিদ্ধান্ত ভিত্তিক কোনো প্রবন্ধ গবেষণা সাময়িকীতে স্থান করতে পারা অত্যাশ্চর্য ব্যাপারই বলতে হবে।
ম্যাকডোগালের গবেষণার ফলাফল প্রকাশের পর পরই ড. অগাস্টাস পি ক্লার্ক নামের একজন ডাক্তার আমেরিকান মেডিসিন জার্নালে ম্যাকডোগালের কাজের সমালোচনা করে লেখেন যে, ম্যাকডোগাল এখানে খুব স্বাভাবিক অনুকল্পটির কথা ভুলে গেছেন, তা হচ্ছে এই ওজন হ্রাসের (যদি প্রকৃতই ঘটে থাকে) ব্যাপারটাকে বাষ্পীভবনের (evaporation) মাধ্যমে দেহের পানি ত্যাগ দিয়ে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। ব্যাপার হচ্ছে, মৃত্যু পর মুহূর্তে দেহের রক্তসঞ্চালন বন্ধ হয়ে যায়, এবং ফুসফুসের মধ্যকার বাতাস রক্তকে আর ঠাণ্ডা করতে পারে না। ফলে দেহের তাপমাত্রা বেড়ে যায় আর দেহের লোমকূপের মাধ্যমে পানি এভাপোরেট করে বের হয়ে যাওয়ায় ওজন ঘাটতি দেখা যেতে পারে। ড. অগাস্টাস পি ক্লার্কের এই ব্যাখ্যা থেকে এটাও পরিষ্কার হয় কেন কুকুরের ক্ষেত্রে কোনো ওজন হ্রাসের ব্যাপার ঘটে নি। কারণ কুকুর মানুষের মতো ঘামের মাধ্যমে দেহকে ঠাণ্ডা করে না। এ করে প্যান্টিং (panting)-এর মাধ্যমে।
আত্মা নিয়ে আরও অনেকেই বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ব্রুস গ্রেসনের মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতার (near death experience, সংক্ষেপে NDE) পরীক্ষা। দেহ বিচ্যুত আত্মার অস্তিত্বের সপক্ষে আকর্ষণীয় সব অভিজ্ঞতার (Out of Body Experience, সংক্ষেপে OBE) কথা ঢালাওভাবে অনেক মুমূর্ষ রোগী রোগমুক্তির পর বিভিন্ন মিডিয়ায় দাবি করে থাকেন। ব্যাপারগুলো কতটুকু সত্য তা পরীক্ষা করে সত্যাসত্য নির্ণয় করতে চাইলেন ব্রুস গ্রেসন। কীভাবে ব্রুস এ পরীক্ষাটি করলেন সেখানে যাওয়ার আগে এই মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতা বা এনডিই এবং দেহ বিচ্যুত অভিজ্ঞতা বা ওবিই নিয়ে সাধারণ পাঠকদের জন্য কিছু কথা বলে নেওয়া যাক। আমাদের খুব পরিচিত জনের অভিজ্ঞতার কথাই বলি। বেশ ক’বছর আগের কথা। মুক্তমনা সদস্য এবং এই বইয়ের সহলেখক অভিজিৎ রায়ের জীবন সাথী বন্যা একবার গাড়িতে উঠতে গিয়ে গাড়ির দরজার সাথে মাথায় টক্কর লেগে দারুণ আঘাত পেলেন। গাড়িতে উঠে বলতে লাগলেন। তার সারা গা নাকি অবশ হয়ে যাচ্ছে। বিপদের কথা। তাড়াতাড়ি তাকে হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যাওয়া হলো। চেতন-অচেতনের মাঝামাঝি কোনো এক স্টেটে ছিল সেসময়টা (পরে বলেছিলেন সারাটা সময় নাকি তার মনে হচ্ছিল সে মারা যাচ্ছে, যদিও তার মনে হয়েছিল মৃত্যু ব্যাপারটা তেমন ভয়ানক কিছু না)। হয়ত কিছু সময়ের জন্য জ্ঞানও হারিয়ে থাকতে পারেন। তিনি। ভালো যে, হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নেওয়ার পর ডাক্তারদের সেবাযত্নে কিছুক্ষণের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে পেলেন। একটু পরে দিব্যি সুস্থ সবল হয়ে বাসায় ফিরে এলেন। কিন্তু হাসপাতালে ওই আধো জাগা আধো অচেতন অবস্থার মধ্যে এক বিরল অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফেললেন তিনি। এই অভিজ্ঞতার কথা তিনি এখনও সুযোগ পেলেই বলে বেড়ান। তিনি দেখছিলেন (নাকি বলা উচিত ‘অনুভব করেছিলেন), তিনি নাকি দেহ থেকে বিযুক্ত হয়ে সারা কক্ষ জুড়ে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছেন। তার কোনো ওজন নেই। হালকা পালকের মতো হয়ে গেছেন তিনি। ওভাবে ভেসে ভেসেই হাসপাতালে ডাক্তার-নার্সদের শঙ্কিত মুখগুলোও পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন। সারা ঘরের কোথায় কী আছে সবই দেখছিলেন উপর থেকে। টেবিলে রাখা পানির গ্লাস, বিছানার এলোমেলো চাঁদর, চিন্তিত লোকজনের মুখ, সবকিছু সাইকোলজিস্টরা এ অবস্থাকেই বলেন ‘আউট অফ বডি এক্সপেরিয়েন্স। বিশ্বাসীরা এগুলোতে আত্মার দেহ-বিচ্যুত অবস্থার অপার্থিব নিদর্শন খুঁজে পান। মুমূর্ষ বা মরণপ্রান্তিক অবস্থাতেই নাকি এ অভিজ্ঞতাগুলো বেশি দেখা যায়। রোগীদের অনেকে এসময় বিরাট বড় টানেলের শেষে আলো দেখা সহ নানা ধরনের আধি ভৌতিক ব্যাপার-স্যাপার প্রত্যক্ষ করেন। কেউ কেউ হাসপাতালের বিছানায় শায়িত চারিদিকে ডাক্তার-নার্স পরিবেষ্টিত নিজের মৃতদেহ পর্যন্ত দেখতে পান। ব্রুস গ্রেসন ঠিক করলেন এ অভিজ্ঞতার গল্পগুলো আসলেই সত্য, নাকি মুমূর্ষ অবস্থায় মনোবৈকল্য, তা একটি সহজ পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখবেন। তিনি তার ল্যাপটপটি সাথে নিয়ে এলেন আর তাতে প্রোগ্রাম করে বিভিন্ন রঙিন ছবি (যেমন, উড়োজাহাজ, নৌকা, প্রজাপতি, ফুল ইত্যাদি) বিক্ষিপ্তভাবে ফুটিয়ে তুললেন। তারপর তিনি ল্যাপটপটিকে স্থাপন করলেন হাসপাতালের হার্টের অস্ত্রোপচার কক্ষের ছাদের কাছাকাছি কোথাও এমন একটা জায়গায় যেখানে অস্ত্রোপচারের সময়। রোগীর দৃষ্টি পৌঁছায় না, কিন্তু দেহবিযুক্ত আত্মা হয়ে সারা কক্ষ ভেসে ভেসে বেড়ালে তা রোগীর দেখতে পাওয়ার কথা। গ্রেসন এনডিই এবং ওডিই’র দাবিদার পঞ্চাশ জন রোগীর ক্ষেত্রে পরীক্ষাটি চালনা করলেন, কিন্তু একজন রোগীও ল্যাপটপের ছবিগুলোকে সঠিকভাবে বর্ণনা করতে পারেন নি[২০৬]। ঠিক একই ধরনের পরীক্ষা স্বতন্ত্রভাবে পরিচালনা করেছিলেন ড. জ্যান হোল্ডেন। তিনিও গ্রেসনের মতোই নেগেটিভ ফল পেলেন[২০৭]
আসলে তাই পাওয়ার কথা। যদি আত্মার মাধ্যমে তথাকথিত পরজগতের সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হতো তবে এই নব্য প্রযুক্তি বিজ্ঞানের জগতে ইতোমধ্যেই বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলত। আমাদের এত দিনের প্রচেষ্টায় বস্তুবাদী ধ্যান ধারণার যে বৈজ্ঞানিক বুনিয়াদ পলে পলে গড়ে উঠেছে তা অচিরেই ধ্বসে পড়তো, বদলে যেত বিবর্তনের মাধ্যমে প্রাণিজগতের এবং সর্বোপরি মানুষের উৎপত্তির সামগ্রিক ধ্যান ধারণা। মানব আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হলে রাতারাতি তা প্রকৃতিতে মানুষকে প্রদান করত এক অভূতপূর্ব বিশিষ্টতা। কিন্তু তা হয় নি। বরং বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক সময়ের সকল আবিষ্কার গেছে এই মানবকেন্দ্রিক ধারণার বিপরীতে। কোপার্নিকাস প্রমাণ করেছিলেন আমাদের আবাসভূমি পৃথিবী নামের গ্রহটি কোনো বিশিষ্ট গ্রহ নয়, এটি না মহাবিশ্বের না এ সৌরজগতের কেন্দ্র। বরং লক্ষ কোটি গ্রহ তারকার ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া সামান্য গ্রহ ছাড়া এটি কিছু নয়। এ যেন ছিল সনাতন চিন্তাভাবনার পিঠে এক রূঢ় চাবুক। এতদিনকার প্রচলিত রূপকথা, উপকথা আর ধর্মগ্রন্থের বাণীতে পৃথিবী যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল তা কোপার্নিকাসের এক চাবুকে যেন লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। তারপর ডারউইন এসে কষলেন আরেক দফা চাবুক। তিনি দেখালেন, এ পৃথিবীর মতো এর বাসিন্দা মানুষও কোনো বিশেষ সৃষ্টি নয়, বরং অন্যান্য প্রাণীকুলের মতোই দীর্ঘদিনের ক্রমবিবর্তনের ফল। এতদিন ধরে মানুষ নিজেকে সৃষ্টির কেন্দ্রস্থলে বসিয়ে, নিজেকে ঈশ্বরের আপন প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট ভেবে যে বিশ্বাস স্থাপন করে এসেছিল, ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের ধাক্কায় সেই বিশ্বাসের অট্টালিকা যেন তাসের ঘরের মতোই ভেঙে পড়ল। পরবর্তীকালে আলেকজান্ডার ওপারিন, হাল্ডেন, ইউরে-মিলার, সিডনি ফক্সের ক্রমিক গবেষণা বিবর্তনকে নিয়ে গেল সূক্ষ রাসায়নিক স্তরে-যা অজৈব পদার্থ থেকে জৈব পদার্থের উন্মেষকে (অজৈবজনি) বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে দিল। বস্তুত বৈজ্ঞানিক সমাজে অজৈবজনি এবং বিবর্তন তত্ত্বের প্রতিষ্ঠার পর থেকে মানুষ আত্মার অস্তিত্ব ছাড়াই জীবনের উৎপত্তি, বিকাশ ও বিবর্তনকে ব্যাখ্যা করতে পারে। কৌতূহলী পাঠকেরা এ বিষয়ে আরও জানতে চাইলে বিবর্তনের পথ ধরে’ (অবসর, ২০০৭) এবং মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে (অবসর, ২০০৭) বই দুটি পড়ে দেখতে পারেন।
কিন্তু তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে আত্মা যদি নাই থাকল, বিভিন্ন জনের মরণপ্রান্তিক অভিজ্ঞতাগুলোকে (এনডিই এবং ওডিই) কীভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? ওই যে হাসপাতালে শুয়ে শুযে যে দেখতে পায় তারা হাসপাতালের কক্ষ জুড়ে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে? এরা কি সবাই তবে মিথ্যে বলছে? না মোটেও তা নয়। আর। তাছাড়া ওভাবে সবাইকে মিথ্যেবাদী বানাতে গেলে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়ের’ দশা হবে। কারণ এধরনের ওডিই অভিজ্ঞতাপ্রাপ্ত মানুষের সংখ্যা এ পৃথিবীতে নেহাত কম। তো নয়। দেহ থেকে বের হয়ে ভেসে ভেসে বেড়ানোই কেবল নয়, কেউ এ সময় টানেলের শেষপ্রান্তে উজ্জ্বল আলো দেখতে পায়, কেউবা মৃত লোকজনের (যেমন সন্ত, যিশুখ্রিস্ট, মুহাম্মদ, ফেরেশতা, মৃত আত্মীয়স্বজন প্রভৃতি) দেখা পায়। একটি পরিসংখ্যানে দেখা গেছে আমেরিকার শতকরা প্রায় ১৫-২০ ভাগ লোক মনে করে তাদের জীবনের কোনো না কোনো সময় ওডিই বা এনডিই এর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এগুলোর কী ব্যাখ্যা?
এর ব্যাখ্যা অবশ্যই আছে, এবং তা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানেই বেরিয়ে এসেছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন মস্তিষ্ক আমাদের দেহের এক অতি জটিল অঙ্গ। কী রকম জটিল একটু কল্পনা করা যাক। মস্তিষ্কের জটিলতাকে অনেক সময় মহাবিশ্বের জটিলতার সাথে তুলনা করা হয়ে থাকে। কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্র ছড়িয়ে ছিটিযে থেকে আমাদের পরিচিত সুবিশাল এই মহাবিশ্বে তৈরি হয়েছে বিশাল বপুর সব সৌরজগৎ কিংবা ছায়াপথের। ঠিক একই রকমভাবে বলা যায়, আমাদের করোটির ভেতরে প্রায় দেড় কিলো ওজনের এই থকথকে ধূসর পদার্থটির মধ্যে গাদাগাদি করে লুকিয়ে আছে প্রায় দশ হাজার কোটি নিউরন আর কোটি কোটি সান্যাপসেস; আর সেই সাথে সেরিব্রাম, সেরিবেলাম, ডাইসেফেলন আর ব্রেইনস্টেমে বিভক্ত হয়ে তৈরি করেছে জটিলতম সব কাঠামোর। ২০০২ সালে পিএইচডি-র কাজের অংশ হিসেবে যখন মানব মস্তিষ্কের মডেলিং করতে হয়েছিল তখন ব্রেনের প্রায় তেতাল্লিশটি কাঠামো বা প্রত্যঙ্গ শনাক্ত করে মডেলিং করেছিলাম[২০৮]। সেগুলোর ছিল বিদঘুটে সমস্ত নাম কর্পাস ক্যালোসাম, ফরনিক্স, হিপোক্যাম্পাস, হাইপোথ্যালমস, ইনসুলা, গাইরাস, কডেট নিউক্লিয়াস, পুটামেন, থ্যালামাস, সাবস্ট্যানশিয়া নায়াগ্রা, ভেন্ট্রিকুলাস ইত্যাদি। আমাদের চিন্তাভাবনা, কর্মকাণ্ড, চালচলন এবং প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা অনেকাংশেই মস্তিষ্কের এই সমস্ত বিদঘুটে নামধারী প্রত্যঙ্গগুলোর সঠিক কর্মকাণ্ডের এবং তাদের কাজের সমন্বযের ওপর নির্ভরশীল। দেখা গেছে, মস্তিষ্কের কোনো অংশ আঘাতপ্রাপ্ত হলে, কিংবা এর কাজকর্ম বাধাগ্রস্ত হলে নানারকমের অদ্ভুতুড়ে এবং অতীন্দ্রিয় অনুভূতি হতে পারে।
যেমন, কর্পাস ক্যালোসাম নামের গুরুত্বপূর্ণ কাঠামোটি মস্তিষ্কের বামদিক এবং ডানদিকের কাজের সমন্বয় সাধন করে থাকে। আমরা সবাই জানি যে, আমাদের ব্রেন একটি হলেও এটি মূলত ডান এবং বাম-এই দুই গোলার্ধে বিভক্ত। এই দুই গোলার্ধকে আক্ষরিক অর্থেই আটকে রাখে দুই গোলার্ধের ঠিক মাঝখানে বসে থাকা কর্পাস ক্যালোসাম নামের প্রত্যঙ্গটি কোনো কারণে মাথার মাঝখানের এই অংশটি আঘাতপ্রাপ্ত হলে মাথার বামদিক এবং ডানদিকের সঠিক সমন্বয় ব্যাহত হয়। ফলে রোগীর দ্বৈতসত্বর (Split Brain experience) উদ্ভব ঘটতে পারে।
ষাটের দশকে রজার স্পেরি, উইলসন এবং মাইকেল গ্যাজানিগার বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বেরিয়ে আসে মজার মজার সব তথ্য। দেখা গেল এধরনের রোগীদের। মাথার বামদিক এক ধরনের চিন্তা করছে তো ডানদিক করছে আরেক ধরনের চিন্তা[২০৯]। মাথার দুই ভাগই আলাদা আলাদাভাবে কনশাস বা চেতনামযা মাথার। বাম অংশ পেশাগত জীবনে ড্রাফটসম্যান হতে চায়, তো ডান অংশ হতে চায় রেসিং ড্রাইভার[২১০]! এখন যারা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী, তাদের কাছে সহজেই এ প্রশ্নটি উত্থাপন করা যায়, মস্তিষ্ক-বিভক্ত দ্বৈতসত্বধারী রোগীদের দেহে কি তাহলে দুটি আত্মা বিরাজ করছে? বাড়তি আত্মাটি তাহলে দেহে কোত্থেকে এলো? বোঝাই যাচ্ছে, আত্মার অস্তিত্ব দিয়ে এই ঘটনার ব্যাখ্যা মেলে না, এর ব্যাখ্যা সঠিকভাবে দিতে পারে ‘দ্বিখণ্ডিত মস্তিষ্ক এবং মাথার মাঝখানে থাকা কর্পাস ক্যালোসাম নামের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের কাজকর্ম।
ছবি। পেজ ২৩১
চিত্র : এই বইয়ের সহলেখক অভিজিৎ রায়কে পিএইচডির কাজের অংশ হিসেবে মানব মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ শনাক্ত করে ত্রি-মাত্রিক মডেলিং করতে হয়েছিল। ৪৩টি অংশ সঠিকভাবে শনাক্ত করে মডেলিং করেছিলেন তিনি। উপরের ছবিতে সেই মডেলিং-এর অংশবিশেষ দেখানো হয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, আমাদের চিন্তাভাবনা, কর্মকাণ্ড, চালচলন এবং প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা অনেকাংশেই মস্তিষ্কের এই সমস্ত প্রত্যঙ্গগুলোর সঠিক কর্মকাণ্ডের এবং তাদের সমন্বয়ের ওপর নির্ভরশীল।
আবার বিজ্ঞানীরা এও দেখেছেন, হাইপোথ্যালামাস নামে মস্তিষ্কের আরেকটি প্রত্যঙ্গকে কৃত্রিমভাবে বৈদ্যুতিক উদ্দীপ্ত করে (মূলত মৃগীরোগ সারাতে এ প্রক্রিয়াটি ব্যবহৃত হতো) দেহবিচ্যুত অবস্থার সৃষ্টি করা যায়, অন্তত রোগীরা মানসিকভাবে মনে করে যে সে দেহ বিযুক্ত হয়ে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। এধরনের অবস্থা সৃষ্টি হয় মস্তিষ্কে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে (হাইপারকার্বিয়া) কিংবা কোনো কারণে রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে (হাইপক্সিয়া)। কিছু কিছু ড্রাগ যেমন, ক্যাটামিন, এলএসডি, সিলোকারপিন, মেকালিন প্রভৃতির প্রভাবে নানা ধরনের অনুভূতির উদ্ভব হয় বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ সমস্ত ড্রাগের প্রতিক্রিয়া হিসেবে অচৈতন্যাবস্থা থেকে শুরু করে দেহ বিযুক্ত অনুভূতি, আলোর ঝলকানি দেখা, পূর্বজন্মের স্মৃতি রোমন্থন, ধর্মীয় অভিজ্ঞতা সবকিছুই পাওয়া সম্ভব। এক ভদ্রলোককে চিনতাম যিনি যিশুখ্রিস্টকে দেখার এবং পাওয়ার জন্য এলএসডি সেবন করতেন। আমাদের আরেক বন্ধু প্রথমবারের মতো গাঁজা থেযে এমন সব কাণ্ড করা শুরু করেছিল যা মনে পড়লে এখনও হাসি পায়। হাড় কাঁপানো শীতের রাতে ‘গরমে পুইড়া যাইতাছি’, ‘আমারে হাসপাতালে নিয়া যা’ বলে হাউ মাউ কাঁদতে আর চ্যাঁচ্যাঁতে লাগলো। আমাদের তখন সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ ব্যস, কলেজ পালিয়ে ‘গাঁজা খেলে কেমন লাগে’ এই রহস্য উদঘাটনে আমরা তখন ব্যস্ত। ভযই পেয়ে গিয়েছিলাম সে রাতে। যদিও শেষটায় বন্ধুটিকে হাসপাতালে নিতে হয় নি, কিন্তু পরদিন তার পাংশু মুখের দিকে তাকিযেই বুঝেছিলাম কী ধকলটাই গেছে। তার ওপর দিয়ে সারা রাত। সবাই মিলে চেপে ধরায় সে বলেছিল, ‘সারা রাত আমি শুধু দেখছিলাম আমি একটা নিকষ কালো অন্ধকার টানেলের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছি, আর সবকিছু আমার ওপরে ভেঙে পড়ছে। গরম গরম বলে চ্যাঁচাঁচ্ছিলি কেন-এ প্রশ্ন করায় বলেছিল, তার নাকি মনে হয়েছিল টানেলের শেষেই দোজখের আগুন, সে আগুনে নাকি তাকে পুড়িয়ে ঝলসিযে কাবাব বানানো হবে! বলা বাহুল্য, উদাহরণ থেকে বোঝা যায়, মরণ প্রান্তিক এবং দেহ-বিযুক্ত অনুভূতিগুলো আসলে কিছুই নয়, আমাদের মস্তিষ্কেরই স্নায়বিক উত্তেজনার ফসল। আর এজন্যই শ্মশানঘাটের কোনো কোনো সাধু-সন্ন্যাসী কেন গাঁজা, চরস, ভাং থেযে মা কালীকে পেয়ে গেছি’ ভেবে নাচানাচি করে, তা বোঝা যায়।
এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী সুজান ব্ল্যাকমোরের কথা বলা যেতে পারে। সুজান ব্ল্যাকমোর মরণ-প্রান্তিক অভিজ্ঞতা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ একজন মনোবিজ্ঞানী, ইংল্যান্ডের ওযেস্ট ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক। এক সময় টেলিপ্যাথি, ইএসপি, পরামনোবিদ্যায় বিশ্বাসী থাকলেও, আজ তিনি এ সমস্ত অলৌকিকতা, ধর্ম এবং পরজগৎ সম্বন্ধে সংশয়ী। সংশয়ী হয়েছেন নিজে বৈজ্ঞানিকভাবে এগুলোর অনুসন্ধান করেই। তিনি ‘ডাইং টু লিভ’, ‘ইন সার্চ অফ দ্য লাইট’ এবং ‘মিম মেশিন’ সহ বহু বইয়ের প্রণেতা। তিনি তার ডাইং টু লিভ : নিযার ডেথ এক্সপেরিয়েন্স (১৯৯৩) বইয়ে উল্লেখ করেছেন অক্সফোর্ডে অধ্যয়নকালীন (সত্তুরের দশকে) তিন বন্ধুর সাথে মিলে মারিজুয়ানা সেবন করে কীভাবে একদিন তার ‘আউট অব বডি’ অভিজ্ঞতা হয়েছিল, কীভাবে তিনি টানেলের মধ্য দিয়ে ভেসে ভেসে বেড়িয়েছিলেন, অক্সফোর্ডের বিল্ডিঙের বাইরে ভাসতে ভাসতে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে নিউইয়র্কে পৌঁছে গিয়েছিলেন, তারপর আবার নিজের দেহে ফিরে গিয়েছিলেন[২১১]। তার এ অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতার কাহিনি লিপিবদ্ধ করে রাখা আছে ‘The Archives of Scientists Transcendent Experiences (TASTE) ওযেবসাইটে[১১২]। কিন্তু সুজান ব্ল্যাকমোর যা করেন নি তা হলো অন্যান্য ধর্মান্ধ ব্যক্তিবর্গের মতো ‘ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতার অপার মহিমায় আপ্লুত হয়ে যাওয়া, কিংবা এ ঘটনার পেছনে অকাট্য প্রমাণ হিসেবে স্রষ্টা, আত্মা কিংবা পরজগতের অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া। বরং তিনি যুক্তিনিষ্ঠভাবে এনডিই এবং ওবিই-এর বৈজ্ঞানিক কারণ অনুসন্ধান করেছেন এবং উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, মরণ প্রান্তিক অভিজ্ঞতাগুলো কোনো পরকালের অস্তিত্বের প্রমাণ নয়, বরং এগুলোকে ভালোমতো ব্যাখ্যা করা যায় স্নায়ু-রসায়ন, শরীরবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞান থেকে আহরিত জ্ঞানের সাহায্যে।
ছবি। পেজ ২৩৪
চিত্র : মরণ প্রান্তিক অভিজ্ঞতার সময় অনেকেই টানেল বা সুরঙ্গ দেখে থাকেন
কেন মরণ প্রান্তিক অভিজ্ঞতাগুলোতে কেবলই টানেল বা সুরঙ্গ দেখা যায়? বিশ্বাসীরা বলেন, ওটি ইহজগৎ আর পরজগতের সংযোগ পথ। টানেলের পেছনে আলোর দিগন্ত আসলে পরজগতের প্রতীকী রূপ। কিন্তু তাহলে অবধারিতভাবে প্রশ্নের উদয় হয় কেন কেবলই সুরঙ্গ? কেন কথনও দরজা নয় কিংবা নয় কোনো বেহেস্তি কপাট কিংবা নয় গ্রিক মিথোলজির আত্মা পারাপারের সেই ‘রিভার স্ট্যাক্স’? এখানেই সামনে চলে আসে আধ্যাত্মিকতার সাথে বিজ্ঞানের বিরোধের প্রশ্নটি। বিজ্ঞানীরা বলেন, ‘সুরঙ্গ দর্শন’ আসলে মরণ প্রান্তিক কোনো ব্যাপার নয়, নয় কোনো অপার্থিব ইঙ্গিত। সেজন্যই মরণ প্রান্তিক অবস্থার বাইরেও মৃগীরোগ, মাইগ্রেনের ব্যথার সময় অনেকে সুরঙ্গ দেখে থাকতে পারেন। বিশেষজ্ঞরা বলেন, সুরঙ্গ দেখা যেতে পারে মস্তিষ্ক যখন থাকে খুবই ক্লান্ত, শ্রান্ত, কিংবা কোনো কাজে যখন চোখের ওপর অত্যধিক চাপ পড়ে। আবার কখনও সুরঙ্গ দেখা যেতে পারে এলএসডি, সাইলোকিবিন কিংবা মেকালিনের মতো ড্রাগ-সেবনে। আসলে স্নায়ুজ-কল্লোল (Neural Noise) এবং অক্ষীয়-করটিকাল জরিপণের (Retino Cortical Mapping) সাহায্যে টানেলের মধ্য দিয়ে আঁধার থেকে আলোতে প্রবেশের অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করা যায়[২১৩]। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ুজীববিজ্ঞানী জ্যাক কোয়ান (Jack Cowan) ১৯৮২ সালে পুরো প্রক্রিয়াটিকে একটি বৈজ্ঞানিক জার্নালে গাণিতিক মডেলের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন[২১৪]। তার মডেলের সাহায্যে কোয়ান দেখিয়েছেন, কর্টেক্সে ডোরা দাগ থাকলে তা আমাদের চোখে অনেকটা সর্পিল কুণ্ডলী (Spirals) আকারে রূপ নেবে। এগুলো আমরা ছোটবেলায় ‘দৃষ্টি বিভ্রমের’ (Visual Illusion) উদাহরণ হিসেবে দেখেছি। নিচে পাঠকদের জন্য এমনই একটি ছবি দেওয়া হলো। ছবিটি দেখুন। বক্ররেখাগুলোকে সর্পিলাকার কুণ্ডলী বলে বিভ্রম হবে। যদিও বাস্তবতা হলো, বক্ররেখাগুলো একেকটি বৃত্ত।
মরণ প্রান্তিক অভিজ্ঞতা লাভের সময় প্রায় একই রকম বিভ্রম ঘটে মস্তিষ্কের মধ্যেও। ড্রাগ সেবনের ফলে কিংবা অত্যধিক টেনশনে কিংবা অন্য কোনো কারণে রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে ভিজুয়াল কর্টেক্সের গতিপ্রকৃতি সতত বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে এ সময় ব্যক্তিরা নিজেদের অজান্তেই টানেল-সদৃশ প্যাটার্নের দর্শন পেযে থাকেন। এটাই সুরঙ্গ-দর্শনের মূল কারণ। সুরঙ্গ দর্শনের এই স্নায়ুজ-কল্লোল এবং অক্ষীয়-করটিকাল জরিপণের গাণিতিক মডেলটির পরবর্তীকালে আরও উন্নতি ঘটান পল ব্রেসলফ, সুজান ব্ল্যাকমোর এবং ট্রস্কিয়াস্কো এবং অন্যান্যরা[২১৫]।
ছবি। পেজ ২৩৭
চিত্র : বক্ররেখাগুলোকে সর্পিলাকার কুণ্ডলীর টানেল বলে বিভ্রম হচ্ছে। যদিও বাস্তবতা হলো, বক্র রেখাগুলো একেকটি বৃত্ত। প্রমাণ হিসেবে ওগুলোর ওপর আঙুল ঘুরিয়ে দেখতে পারেন।
ছবি। পেজ ২৩৮
চিত্র : স্নায়ুজ-কল্লোল এবং অক্ষীয়-করটিকাল জরিপণের সাহায্যে সুরঙ্গ দর্শনের অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করা যায়।
কাজেই বোঝা যাচ্ছে সুরঙ্গ-দর্শনের মাঝে অলৌকিক বা অপার্থিব কোনো ব্যাপার নেই, নেই কোনো পারলৌকিক রহস্য, যা আছে তা একেবারে নিরস, নিখাঁদ বিজ্ঞান। বলা বাহুল্য, সত্যজিৎ রায়ের ফেলু মিত্তিরের গোয়েন্দা গল্পের মতো ‘সুরঙ্গ-রহস্য’ শেষ পর্যন্ত সমাধান করেছে বিজ্ঞানীরাই। শুধু রহস্য সমাধান নয়, গাণিতিক মডেল টডেল করাও সারা। শুধু তাই নয়, টানেলের পাশাপাশি কেন যিশুখ্রিস্ট কিংবা মৃত-আত্মীয়স্বজনের দেখা পাওয়া যাচ্ছে তারও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলেন, ব্যাপারটা হয়ত পুরোটাই সমাজ-সাংস্কৃতিক। যিশুখ্রিস্টের দেখা পান তারাই, যারা দীর্ঘদিন খ্রিস্টীয় আবহাওয়ায় বড় হয়েছেন, বাবা মা, শিক্ষক, পাড়া পড়শিদের কাছ থেকে ‘খ্রিস্টীয় ধ্যানধারণা পেয়েছেন। একজন হিন্দু কথনোই মরণ প্রান্তিক অভিজ্ঞতায় খ্রিস্টের দেখা পান না, তিনি পান বিষ্ণু, ইন্দ্র বা লক্ষীর দেখা, আর না হলে ‘যমদূতেরা আবার একজন মুসলিম হত সেক্ষেত্রে দর্শন লাভ করেন আজরাইল ফেরেশতার। বোঝা। যাচ্ছে, ধর্মীয় দিব্য দর্শন’ কোনো সর্বজনীন সত্য নয়, বরং, আজন্ম লালিত ধর্মানুগত্য আর নিজ নিজ সংস্কৃতির রকমফেরে ব্যক্তিবিশেষে পরিবর্তিত হয়। কাজেই, ঈশ্বর দর্শনই বলুন আর ধর্মীয় দিব্য দর্শন’ই বলুন, এগুলোর উৎসও আসলে মানব মস্তিষ্কই। দেখা গেছে মস্তিষ্কের কোনো কোনো অংশকে উত্তেজিত করলে মানুষের পক্ষে ভূত, প্রেত, ড্রাকুলা থেকে শুরু করে শ্যতান, ফেরেশতা কিংবা ঈশ্বর দর্শন সবকিছুই সম্ভব। এ ব্যাপারটা আরও বিশদভাবে বুঝতে হলে আমাদের মস্তিষ্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ-’টেম্পোরাল লোব সম্বন্ধে জানতে হবে।
.
টেম্পোরাল লোব : মস্তিষ্কের ‘গড স্পট’?
বিশ্বের তাবৎ বিজ্ঞানী আর গবেষকের দল অনেকদিন ধরেই সন্দেহ করছিলেন, ঈশ্বর দর্শন, দিব্যদর্শন, কিংবা ওহি প্রাপ্তির মতো ধর্মীয় অভিজ্ঞতাগুলো আসলে স্রেফ মস্তিষ্কজাত? সেই ১৮৯২ সালের আমেরিকার পাঠ্যপুস্তকগুলোতেও এপিলেন্সির সাথে ‘ধর্মীয় আবেগের সাযুজ্য খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছিল। ব্যাপারটা আরও ভালোমতো বোঝা গেল বিগত শতকের মধ্যবর্তী সময়ে। ১৯৫০ সালের দিকে উইল্ডার পেনফিল্ড নামের এক নিউরোসার্জন মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করার সময় ব্রেনের মধ্যে ইলেকট্রোড ঢুকিযে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশকে বৈদ্যুতিকভাবে উদ্দীপ্ত করে রোগীদের কাছে এর প্রতিক্রিয়া জানতে চাইতেন। যখন কোনো রোগীর ক্ষেত্রে ‘টেম্পোরাল লোব’ (ছবিতে দেখুন)–এ ইলেকট্রোড ঢুকিযে উদ্দীপ্ত করতেন, তাদের অনেকে নানা ধরনের গাযেবি আওয়াজ শুনতে পেতেন, যা অনেকটা ‘দিব্য দর্শনের অনুরূপ[২১৬]। এই ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হলো, ১৯৭৫ সালে যখন বোস্টন ভেটেরান্স অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হাসপাতালের স্নায়ু-বিশেষজ্ঞ নরমান গেসচ উইন্ড-এর গবেষণায় প্রথমবারের মতো এপিলেপ্সি বা মৃগীরোগের সাথে টেম্পোরাল লোবে বৈদ্যুতিক মিসফায়ারিং-এর একটা সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেল। একই ক্রমধারায় ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নায়ু-বিশেষজ্ঞ ভিলায়ানুর এস রামাচান্দ্রন তার গবেষণায় দেখালেন, টেম্পোরাল লোব এপিলেপ্সি রোগীদের ক্ষেত্রেই ঈশ্বর-দর্শন, ওহি প্রাপ্তির মতো ধর্মীয় অভিজ্ঞতার আস্বাদনের সম্ভাবনা বেশি]২১৭]। এগুলো থেকে হয়ত অনুমান করা যায়, কেন আমাদের পরিচিত ধর্ম প্রবর্তকদের অনেকেই ‘ওহি প্রাপ্তির আগে ‘ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেতেন’, ‘গায়েবি কণ্ঠস্বর শুনতে পেতেন, তাদের ‘কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসত’ কিংবা তারা ‘ঘন ঘন মূৰ্ছা যেতেন[২১৮]।
ছবি। পেজ ২৪১
চিত্র : মস্তিষ্কের টেম্পোরাল লোব : অনেক বিজ্ঞানীই মনে করেন মস্তিষ্কের এই অংশটিই হয়ত ধর্মীয় প্রণোদনার মূল উৎস। এই অংশটি নিয়ে গবেষণা করে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আধ্যাত্মিকতার সাথে এপিলেপ্পির জোরালো সম্পর্কও পাওয়া গেছে।
এই ধরনের গবেষণা থেকে পাওয়া ফলাফলে উদ্বুদ্ধ হয়ে কানাডার লরেন্টিয়ান ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক মাইকেল পারসিঙ্গার আরও একধাপ সাহসী গবেষণায় হাত দিলেন। তিনি ভাবলেন, টেম্পোরাল লোবে বৈদ্যুতিক তারতম্য যদি ধর্মীয় প্রণোদনার উৎস হয়েই থাকে তবে, উল্টোভাবে মস্তিষ্কের এই গোদা অংশটিকে উদ্দীপ্ত করেও তো কৃত্রিমভাবে ধর্মীয় প্রণোদনার আবেশ আস্বাদন করা সম্ভব, তাই না? হ্যাঁ, অন্তত তাত্ত্বিকভাবে তো তা সম্ভব। ড. পারসিঙ্গার ঠিক তাই করলেন। তিনি টেম্পোরাল লোবকে কৃত্রিমভাবে উদ্দীপ্ত করে ধর্মীয় আবেশ পাওয়ারজন্য তৈরি করলেন তার বিখ্যাত ‘গড হেলমেট’। এই হেলমেট মাথায় পরে বসে থাকলে নাকি ‘রিলিজিয়াস এক্সপেরিয়েন্স’ আহরণ করা সম্ভব। হেলমেট বানানোর পর অফিশিয়ালি প্রায় ছ’শ জনকে এটি পরিয়ে পরীক্ষা চালানো হয়েছে। এদের প্রায় ৮০ শতাংশ বলেছেন, তাদের এক ধরনের অপার্থিব অনুভূতি হয়েছে[২১৯]। তারা অনুভব করেছেন, কোনো অশরীরী কেউ (কিংবা কোনো স্পিরিট) তাদের ওপর নজরদারি করেছে। অনেকের অভিজ্ঞতার মাত্রা এর চেয়েও বেশি। যেমন, এক নারী হেলমেট পরার পর মনে হয়েছে তিনি তার মৃত মাযের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। আরেক নারীর কাছে এই অশরীরী অস্তিত্ব এতটাই প্রবল ছিল যে, পরীক্ষার শেষে যখন অশরীরী আত্মা হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিল, তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন। হেলমেট মাথায় পরার পর ব্রিটিশ সাংবাদিক আযান কটনের পুরো সময়টা নিজেকে তিব্বতি ভিক্ষু বলে বিভ্রম হয়েছিল। বিজ্ঞানী সুজান ব্ল্যাকমোরের অভিজ্ঞতাটাই বোধহয় এক্ষেত্রে সবচেয়ে মজার। তিনি নিউ সায়েন্টিস্ট পত্রিকায় নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এভাবে[২২০]
আমার হঠাৎ মনে হলো কেউ আমার পা ধরে টানছে, দুমড়ে মুচড়ে নষ্ট করে দিচ্ছে, তারপর ধাক্কা মেরে আমাকে দেওয়ালে ফেলে দিল। পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত; কিন্তু ঘটনাটা ছিল দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। আমার প্রথমে প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল, পরে রাগের স্থান ক্রমান্বয়ে দখল করে নিল ভীতি…।
অধ্যাপক ব্ল্যাকমোর পরে বলেছিলেন, ‘পারসিঙ্গারের ল্যাবরেটরিতে আমার সঞ্চিত অভিজ্ঞতা এক কথায় অবিস্মরণীয়। পরে যদি বেরিয়ে আসে কোনো প্ল্যাসিবো এফেক্টের কারণে আমি এগুলোর মধ্য দিয়ে গেছি, তাহলে অবাকই হবো।”
তবে সবার ক্ষেত্রেই যে ‘গড হেলমেট একই রকমভাবে কাজ করেছে তা কিন্তু নয়। একবার গড় হেলমেটের কার্যকারিতা দেখানোর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্সকে। ডকিন্স বিবর্তনবাদে বিশেষজ্ঞ একজন বিজ্ঞানী, পাশাপাশি সবসময়ই ধর্ম, অলৌকিকতা প্রভৃতি বিষয়ে উৎসুক। ধর্মের একজন কঠোর সমালোচক তিনি। নিজেকে কখনোই নাস্তিক হিসেবে পরিচিত করতে পরোয়া করেন না। ঈশ্বরে বিশ্বাস তার কাছে বিভ্রান্তি বা ডিলুশন’, ধর্মের ব্যাপারটা তার কাছে ‘ভাইরাস’। এহেন ব্যক্তিকে হেলমেট পরিয়ে তার মনের মধ্যে কোনো ধরনের ধর্মীয় অনুভূতি’ ঢোকানো যায় কিনা, এ নিয়ে অনেকেই খুব উৎসুক ছিলেন।
ছবি। পেজ ২৪৪
চিত্র : মাইকেল পারসিঙ্গার উদ্ভাবিত ‘গড হেলমেট’
রিচার্ড ডকিন্স খুব আগ্রহভরেই এই পরীক্ষায় ‘গিনিপিগ’ হতে রাজি হলেন ২০০৩ সালে। ডকিন্স পারসিঙ্গারের ল্যাবরেটরিতে এসে হেলমেট পরে চেম্বারে ঢুকলেন। যথা সময় বেরিযেও আসলেন। এসে বিবিসির সাথে সাক্ষাৎকারে বললেন, ‘আমি খুবই হতাশ। খুব ইচ্ছে ছিল ঈশ্বর দর্শনের। কিন্তু চেম্বারে বসে মাথা ঝিম ঝিম করার ভাব ছাড়া আর তো কিছু পেলাম না!’
মনে হচ্ছে ডকিন্সের মতো যুক্তিবাদী মাথা মৃগীরোগের জন্য উপযুক্ত নয়। এদের মতো লোককে বোধহয় সহজে গায়েবি আওয়াজ শোনানো, কিংবা দিব্য দর্শন দেওয়া এত সহজ নয়। কাজেই, দুর্মুখেরা বলবেন, ডকিন্সের মতো নিরেট-মস্তিষ্ক লোকেরা পয়গম্বর হওয়ার উপযুক্ত নন! ধর্মবাদীরা কী আর সাধে বলে যে, নবুয়ত পেতে যোগ্যতা লাগে!!
কিন্তু রিচার্ড ডকিন্সের ওপর কাজ না করলেও এটাও ঠিক সুজান ব্ল্যাকমোরসহ অনেকের মধ্যেই তো করেছে, এবং করেছে খুব ভালোভাবেই তারা নিজেরাই তা স্বীকার করেছেন। আর পারসিঙ্গারের দাবি অনুযায়ী, তার উদ্ভাবিত এ প্রক্রিয়ায় যদি ৮০ শতাংশের বেশি লোকের অপার্থিব অনুভূতি হয়েই থাকে, তবে বলতেই হয় ঈশ্বরানুভূতির মতো ব্যাপারগুলো হয়ত মস্তিষ্কের বাইরে নয়। পারসিঙ্গারের ভাষায[২২১], ঈশ্বর মানুষের মস্তিষ্ক তৈরি করে নি, বরং মানুষের মস্তিষ্কই সৃষ্টি করেছে কথিত শক্তিমান ঈশ্বরের।
.
শেষ কথা
আত্মা ব্যাপারটি মানুষের আদিমতম কল্পনা। এটি সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত নয় এবং আধুনিক বিজ্ঞানের চোখে অপার্থিব আত্মার কল্পনা ভ্রান্তবিশ্বাস ছাড়া কিছু নয়। এ প্রবন্ধে আমরা খুব বিশদভাবে বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে আত্মা নামক ধারণাটিকে যাচাই করার চেষ্টা করেছি। এর থেকে যা বেরিয়ে এসেছে তা হলো আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলোর সাথে ‘আত্মা’ নামক ব্যাপারটি একেবারেই খাপ খায় না। সোজা ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় আত্মার অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ বিজ্ঞান পায় নি। আর যত দিন যাচ্ছে, আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণের আশা ক্রমশ রূপান্তরিত হচ্ছে দুরাশায়। বস্তুত স্নায়ুবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, শরীরবিজ্ঞান, জেনেটিক্স আর বিবর্তন বিজ্ঞানের নতুন নতুন গবেষণা আত্মাকে আক্ষরিক ভাবেই রঙ্গমঞ্চ থেকে হটিয়ে দিয়েছে। আর সেজন্যই যুগল-সর্পিলের (ডিএনএ) রহস্য ভেদকারী নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী ফ্রান্সিস ক্রিক বলেন[২২২], একজন আধুনিক স্নায়ু-জীববিজ্ঞানী মানুষের এবং অন্যান্য প্রাণীর আচরণ ব্যাখ্যা করার জন্য ‘আত্মা’ নামক ধর্মীয় ধারণার দ্বারস্থ হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন না। ১৯২১ সালে বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন একই ধারণা পোষণ করে বলেছিলেন, ‘দেহবিহীন আত্মার ধারণা আমার কাছে একেবারেই অর্থহীন এবং অন্তঃসারশূন্য।
কাজেই বিজ্ঞান মানতে হলে আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী হওয়ার কোনো যুক্তিনিষ্ঠ কারণ নেই। প্রাচীনকালের মানুষেরা জন্ম-মৃত্যুর গূঢ় রহস্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাধান করতে না পেরে আশ্রয় করেছিল ‘আত্মা’ নামক আধ্যাত্মিক ধারণার বিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণা সেসমস্ত পুরনো এবং অসংজ্ঞায়িত ধ্যান ধারণাকে খণ্ডন করে দিয়েছে। আত্মার অস্তিত্ব ছাড়াই বিজ্ঞানীরা আজ মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীর আচরণ, আচার-ব্যবহার এবং নিজের ‘আমিত্ব’ (self) এবং সচেতনতাকে (consciousness) ব্যাখ্যা করতে পারছে। এমনকি খুঁজে পেয়েছে ধর্মীয় অপার্থিব অভিজ্ঞতার বিভিন্ন শরীরবৃত্তীয় উৎস। আমাদের অভিমত হলো-প্রাণের অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা করার জন্য আত্মা একটি অপ্রয়োজনীয় এবং পরিত্যক্ত ধারণা, যেমনই আলোর সঞ্চালনকে ব্যাখ্যা করার জন্য পদার্থবিজ্ঞানীদের চোখে আজ ইথার একটি অপ্রয়োজনীয় এবং পরিত্যক্ত ধারণা। কিন্তু আত্মার সাথে ইথারের পার্থক্য হলো পদার্থবিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে ইথারকে হটানো সম্ভব হলেও আত্মাকে হটানো সম্ভব হয় নি, বরং আত্মা নামক পরিত্যক্ত ধারণাটিই আজও সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয়। অস্তিত্বহীন আত্মার শান্তির জন্য মানুষ তাই কত কিছুই না করে! আর সাধারণ অসচেতন মানুষকে সম্মোহিত রাখতে এই আগাছার চাষকে পুরোদমে জনপ্রিয় করে রেখেছে তাবৎ ধর্মীয় সংগঠনগুলো, স্বীয় ব্যবসায়িক স্বার্থেই। তবে, এমন একদিন নিশ্চয় আসবে যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ জীবন মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করার জন্য আত্মার দ্বারস্থ হবে না; আত্মার ‘পারলৌকিক শান্তির জন্য শ্রাদ্ধ-শান্তিতে কিংবা মিলাদ-মাহফিল বা চল্লিশায় অর্থ ব্যয় করবে না, মৃতদেহকে স্মশান ঘাটে পুড়িয়ে বা মাটিচাপা দিয়ে মৃত দেহকে নষ্ট করবে না, বরং কর্নিয়া, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃৎ, অগ্ন্যাশয় প্রভৃতি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যেগুলো মানুষের কাজে লাগে, সেগুলো মানবসেবায় দান করে দেবে (গবেষণা থেকে জানা গেছে, মানুষের একটিমাত্র মৃতদেহের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে ২২ থেকে পঞ্চাশ জন অসুস্থ মানুষ উপকৃত হতে পারে[২২৩])। এছাড়াও মেডিক্যালের ছাত্রদের জন্য মৃতদেহ উন্মুক্ত করবে ব্যবহারিক ভাবে শারীরবিদ্যা শিক্ষার দু্যার। আরজ আলী মাতুব্বর তার মৃতদেহ মেডিক্যাল কলেজে দান করার সিদ্ধান্ত নিয়ে এক সময় অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন[২২৪]–
..আমি আমার মৃতদেহটিকে বিশ্বাসীদের অবহেলার বস্তু ও কবরে গলিত পদার্থে পরিণত না করে, তা মানব কল্যাণে সোপর্দ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। আমার মরদেহটির সাহায্যে মেডিক্যাল কলেজের শল্যবিদ্যা শিক্ষার্থীগণ শল্যবিদ্যা আয়ত্ত করবে, আবার তাদের সাহায্যে রুগ্ন মানুষ রোগমুক্ত হয়ে শান্তিলাভ করবে। আর এসব প্রত্যক্ষ অনুভূতিই আমাকে দিয়েছে মেডিক্যালে শবদেহ দানের মাধ্যমে মানবকল্যাণের আনন্দ লাভের প্রেরণা।
সে অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে পরবর্তীকালে মেডিক্যালে নিজ মৃতদেহ দান করেছেন ড. আহমেদ শরীফ, ড. নরেন বিশ্বাস, ওয়াহিদুল হক, গায়ক সঞ্জীব চৌধুরী, ফযেজ আহমদ, জ্যোতি বসু প্রমুখ। আমি যখন এ লেখাটি লিখছি সেই তারিখ অনুযায়ী স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বেলাল মোহাম্মদ এ তালিকায় নতুন এবং গর্বিত সংযোজন[২২৫]। সমাজ সচেতন ইহজাগতিক এ মানুষগুলোকে জানাই আমাদের প্রাণের প্রণতি।
৬. বিজ্ঞানময় কিতাব
মুর্খরা সব শোনো, মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনে নি মানুষ কোনো
— কাজী নজরুল ইসলাম
মহাবৈজ্ঞানিক গ্রন্থে স্থির পৃথিবী
এই প্রবন্ধটির সূচনা হয়েছিল একটি নির্দোষ ই-মেইলের জবাব দিতে গিযে। বছর সাতেক আগে আমি (অভিজিৎ রায়) তখন সবে বাংলাদেশ থেকে পাড়ি জমিয়েছি বাইরের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিনা পয়সায় ইন্টারনেট ব্যবহারের আমেজ সামলাতে সময় লাগছে। কুযোর ব্যাঙ-কে কুয়ো থেকে তুলে সমুদ্রে ছেড়ে দিলে যেমন দশা হয় তেমনই দশা তখন আমার কম্পিউটার নামের চার কোনা বাক্সের মাঝে জ্ঞানের অবারিত দু্যার। আমি নাওয়া খাওয়া বাদ দিয়ে পড়ে রইলাম সমুদ্র সিঞ্চনে। এমনই এক সময় সদ্য পরিচিত এক ভদ্রলোকের পাঠানো এক ই-মেইলে এক ওয়েবসাইটের ঠিকানা পেলাম। ঠিকানাটা আসলে একটা অনলাইন পত্রিকার। খুব যে। আগ্রহ নিয়ে গেলাম তা নয়। কিন্তু গিযে অবাকই হলাম। পড়লাম বেশকিছু লেখকের তথ্যবহুল উঁচুমানের লেখা। অজানা অচেনা পত্রিকায় এমন যুক্তিবাদী ইহজাগতিক লেখা? তাও আবার লিখছে কিছু সাহসী বাঙালি। সত্যিই অবাক করার মতো ব্যাপার।
অবশ্য পত্রিকাটিতে সকলেই যে ধর্মের শিকল থেকে মুক্ত হয়ে প্রগতিশীল লেখা লিখতেন বা লিখছেন, তাও নয়। পশ্চিমা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এক ভদ্রলোকের কথা খুব-ই মনে পড়ছে। উনি সবসময়ই একটি বিশেষ প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানের তত্ব খুঁজতেন। এই ফ্যাশনটা ইদানীংকালে বাংলাদেশি শিক্ষিত মুসলমানদের ভেতরে প্রকট আকারে চোখে পড়ছে। বিশেষত দুই বিজ্ঞানী মরিস বুকাইলি এবং কিথ মুরের ‘অবিস্মরণীয় অবদানের পর (ইদানীং সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে তুরস্কের হারুন ইয়াহিয়া নামের আরেক ছদ্ম-বিজ্ঞানী) আজ তারা ১৪০০ বছর আগের লেখা ধর্মগ্রন্থের মধ্যে ‘বিগব্যাং’ খুঁজে পান, মহাবিশ্বের প্রসারণ খুঁজে পান, মানব সৃষ্টির ক্রমবিকাশ খুঁজে পান, অণু পরমাণু, ছায়াপথ, নক্ষত্ররাজি, শ্বেত বামন, কৃষ্ণগহ্বর, ভ্রুণ তত্ব, আপেক্ষিক তত্ব, সুপার স্ট্রিং তত্ব, সবই অবলীলায় পেয়ে যান। তো সেই ভদ্রলোকও বুকাইলি-মুরের প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে কোরআন যে কত ‘সুপার সায়েন্টিফিক বই, তা প্রমাণের জন্যে পাতার পর পাতা লিথে যেতে থাকলেন। আমি অবশেষে তার একটি লেখার প্রতিবাদ করার সিদ্ধান্ত নেই। বলি, কী দরকার আছে এই হাজার বছর আগেকার কতকগুলো সুরার মধ্যে বিগব্যাং-এর তত্ত্ব অনুসন্ধান করার? বিগব্যাং সম্বন্ধে জানতে চাইলে অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের ওপর গাদা গাদা বই বাজারে আছে; দেখুন না ডিফারেন্সিয়াল ইকুযেশন সমাধানের জন্য তো আমাদের গণিতের বই-ই দেখতে হবে, কোরআন হাদিস চষে ফেললে কি এর সমাধান মিলবে? এ যেন বারুদে আগুন লাগলো। উনি এর পরদিন বিশাল মহাভারত আকারের মহাকাব্য লিখে বুঝিয়ে দিলেন ইসলাম এবং বিজ্ঞান বিষয়ে আমার জ্ঞান কত তুচ্ছ; কত নগণ্য, কত অজ্ঞ, কত আহাম্মক আমি। এদিক ওদিক-সেদিক থেকে দৃষ্টান্তের পর দৃষ্টান্ত হাজির করে ‘প্রমাণ করে বুঝিযে পর্যন্ত দিলেন-”দ্যাখ ব্যাটা কোরআনে আধুনিক বিজ্ঞানের সবকিছুই আছে, কোরআন কত বিজ্ঞানময় কিতাব!’
এরপর আমাকেও কি-বোর্ড তুলে নিতে হলো। কী করব, পিঠ যে তখন দেওয়ালে ঠেকে গেছে। বললাম, একটু চোখ-কান খুলে যদি ধর্মগ্রন্থগুলোর ইতিহাসের দিকে তাকানো যায়, তাহলে বোঝা না যাওয়ার তো কথা নয় যে, সেই গ্রন্থগুলো লেখা হয়েছে বহু বছর আগে যখন মানুষের বিজ্ঞানের ওপর দখল এবং জ্ঞান ছিল খুবই সীমিত। এটা আশা করা খুবই বোকামি যে সেই সময়কার লেখা একটা বইয়ের মধ্যে বিগব্যাং-এর কথা থাকবে, সুপার স্ট্রিং-এর কথা থাকবে, আইনস্টাইনের রিলেটিভিটির কথা থাকবে। আধুনিক বিজ্ঞান নয়, ওই সমস্ত বইগুলোতে ফুটে উঠেছে প্রাচীন সমাজ-ব্যবস্থার চালচিত্র, প্রকাশ পেয়েছে তৎকালীন সমাজের মানুষের ধ্যান ধারণা, বিশ্বাস, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা; এর এক চুলও বাড়তি কিছু নয়। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। কোরআন যখন লিখিত হয়েছিল, তখনো গ্যালিলিও, ব্রুনো, কোপার্নিকাসের মতো মনীষীরা এই ধরাধামে আসেননি। তখনকার মানুষদের আসলে জানবার কথা নয় যে তাদের পরিচিত বাসভূমি পৃথিবী নামক এই গ্রহটি যে ‘সূর্য নামক নক্ষত্রের চারিদিকে ক্রমাগত পাক খেয়ে চলেছে। জন্মের পর থেকেই মানুষ। সাদা চোখে সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিমে যেতে দেখেছে, আর রাত হলেই দেখেছে ‘চাঁদ’ কে এর পেছনে পদার্থবিজ্ঞানের কোনো নিয়ম তারা কল্পনা করতে পারে নি, ধরে নিয়েছিল, এগুলো বোধহয় ঈশ্বরের আইন। ঠিক সে কথাগুলোই কোরআন-হাদিস-বেদ-বাইবেলে লেখা আছে। যেমন, ধরা যাক সুরা লুকমান (৩১ : ২৯) এর কথা। এখানে বলা আছে-’আল্লাহই রাতকে দিনে এবং দিনকে রাতে পরিবর্তন করেন, তিনিই সূর্য এবং চন্দ্রকে নিয়মাধীন করেছেন; প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট পথে আবর্তন করে। সূর্য আর চাঁদের এই ভ্রমণের কথা শুধু। সুরা লুকমানে নয়, রয়েছে সুরা ইয়াসিন (৩৬ : ৩৮), সুরা যুমার (৩৯ : ৫), সুরা রা’দ (১৩ : ২), সুরা। আম্বিয়া (২১ : ৩৩), সুরা বাকারা (২ : ২৫৮), সুরা কাফ (১৮ : ৮৬), সুরা ত্বোয়াহায় (২০ : ১৩০)। কিন্তু সারা কোরআন তন্নতন্ন করে খুঁজলেও পৃথিবীর ঘূর্ণনের সপক্ষে একটি আয়াতও মিলবে না। আল্লাহর দৃষ্টিতে পৃথিবী স্থির, নিশ্চল। সুরা নামলে (২৭ : ৬১) পরিষ্কার বলা আছে যে, দুনিয়াকে বসবাসের স্থান করেছেন আর তার মধ্যে নদীসমূহ সৃষ্টি করেছেন আর এটিকে (পৃথিবী) স্থির রাখবার জন্য পাহাড়-পবর্ত সৃজন করেছেন …’। একইভাবে সুরা রুম (৩০ : ২৫), ফাধির (৩৫ : ৪১), লুকমান (৩১ : ১০), বাকারা (২ : ২২), নাহল (১৬ : ১৫) পড়লেও সেই একই ধারণা পাওয়া যায় যে কোরআনের দৃষ্টিতে পৃথিবী আসলে স্থির।
আমি ভদ্রলোককে সবিনয়ে বলেছিলাম, তিনি যদি সত্যিই মনে করেন যে আধুনিক বিজ্ঞানের সকল তত্বই কোরআনে আছে, তাহলে শুধু একটি আয়াত যদি কোরআন থেকে দেখাতে পারেন যেখানে লেখা আছে ‘পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, অথবা নিদেনপক্ষে ‘পৃথিবী ঘুরছে’ আমি তার সকল দাবি মেনে নেব। আরবিতে পৃথিবীকে বলে আরদ’ আর ঘূর্ণন হচ্ছে ‘ফালাক’। একটি মাত্র আয়াত আমি দেখতে চাই যেখানে ‘আরদ’ এবং ‘ফালাক’ পাশাপাশি ব্যবহৃত হয়েছে। উনি দেখাতে পারলেন না।
পারার কথাও নয়। কারণ কোরআনে এধরনের কোনো আয়াত নেই। এর কারণটা আমি আগেই বলেছিতখনকার যুগের মানুষেরা চিন্তা করে তো বের করতে পারে নি পৃথিবীর আহ্নিক আর বার্ষিক গতির কথা। টলেমির পৃথিবীকেন্দ্রিক মতবাদকে মাথা থেকে সরিয়ে কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদে মানুষের চিন্তা ভাবনার উত্তরণ ঘটেছে আসলে আরও অনেক বছর পরে। হযরত মুহাম্মদের যুগে মানুষেরা এমনকি ‘রাত্রিবেলা সূর্য কোথায় থাকে এই রহস্য ভেদ করতে গিযে ‘গলদঘর্ম হয়ে উঠেছিল। পৃথিবী সমতল এ জ্ঞান খাটিয়ে মানুষ তখন ধারণা করত একেবারে শেষ প্রান্তে গিয়ে ‘সূর্যদেব সত্যিই অস্ত যান!’ চিন্তাশীল পাঠকেরা জুলকারনাইনের কথা উল্লেখিত, কোরআনের সেই বিখ্যাত সুরাটিতে চোখ বোলালেই বিষয়টি বুঝতে পারবেন—
অবশেষে যখন সে সূর্যাস্তের দেশে পৌঁছল, সে সূর্যকে এক পঙ্কিল জলাশযে ডুবতে দেখল এবং সেখানে দেখতে পেল এক জাতি। আমি বললাম, হে জুলকারনাইন, হয় এদের শাস্তি দাও, না হয় এদের সাথে ভালো ব্যবহার করো। (১৪ : ৪৬)
যারা কোরআনের মধ্যে অনবরত বিগব্যাং এবং সুপার স্ট্রিং তত্ত্বের খোঁজ করেন, তারা কি একবারের জন্যও ভাবেন না আল্লাহ কেমন করে এত বড় ভুল করলেন! কীভাবে আল্লাহ ভাবলেন যে সূর্য সত্যিই কোথাও না কোথাও অস্ত যায়? কোরআন কি মহা বিজ্ঞানময়’ কিতাব নাকি ভ্রান্তিবিলাস? অনেক পাঠকই হয়ত জানেন না যে মহানবী মুহাম্মদকে শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ ও দার্শনিক বলে অভিহিত করা হয়, তিনি রাতে সূর্য কোথায় থাকে এই রহস্যের কীরকম ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন : এক সাহাবার (আবু জর) সাথে মতবিনিময় কালে মহানবী বলেছিলেন যে, রাত্রিকালে সূর্য থাকে খোদার আরশের নিচে। সারা রাত ধরে সূর্য নাকি খোদার আরশের নিচে থেকে আল্লাহর ইবাদত বন্দেগি করে আর তারপর অনুমতি চায় ভোরবেলা উদযের (সহি বোখারী, হাদিস নং ৬/৬০/৩২৬-৩২৭, ৪/৫৪/৪২১)[২২৬] পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে সূর্য যে আমাদের দৃষ্টির আড়াল হয় (একইভাবে বিপরীতে অবস্থানকারীদের দৃষ্টিগোচর হয়) সেটা ছিল সেসময়ের মানুষের অজানা। কিন্তু তাদের মনে প্রশ্ন ছিল, আর সবসময় ধর্ম যা করে ঠিক তেমনিভাবে অজানা এ প্রশ্নটির উত্তরে আল্লাহকে টেনে এনে সেখানেই সঠিক উত্তর খোঁজার যৌক্তিক পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন নবীজি!
যারা প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলোকে বিজ্ঞানের মোড়কে পুরতে চান, তারা কি এই আয়াতগুলোর কথা জানেন না? অবশ্যই জানেন। জানার পর তারা একটি মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে মনকে শান্ত করেন। অনেকে আবার সেগুলো ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষকে বিভ্রান্ত করেন। আর এখানেই আমাদের আপত্তি। কেবল কোরআনে নয়, অন্য সকল অলৌকিক গ্রন্থেও আমরা নিশ্চল এবং স্থির পৃথিবীর ধারণা পাই। বাইবেল বলে–
‘আর জগতও অটল, তা বিচলিত হবে না’ (ক্রনিকলস ১৬/৩০)
‘জগৎ ও সুস্থির, তা নড়াচড়া করবে না।’ (সাম ৯৩/১) ‘তিনি পৃথিবীকে অনড় এবং অচল করেছেন’ (সাম ৯৬/১০)
‘তিনি পৃথিবীকে এর ভিত্তিমূলের ওপর স্থাপন করেছেন, তা কখনও বিচলিত হবে না’ (সাম ১০৪/৫) ইত্যাদি।
একইভাবে বেদেও রয়েছে–
‘ধ্রুবা দৌবা পৃথিবী ধ্রুবাস : পর্বতা ইমো’ (ঋগ্বেদ দশম মণ্ডল, ১৭৩/৪)
অর্থাৎ, ‘আকাশ নিশ্চল, পৃথিবী নিশ্চল, এ সমস্ত পর্বতও নিশ্চল।
ঋগ্বেদের আরেকটি শ্লোকে রয়েছে–
‘সবিতা যৈন্ত্র : পৃথিবীমর-দগ্ধম্ভনে সবিতা দ্যামদৃং হত।’ (ঋগ্বেদ দশম মণ্ডল, ১৪৯/১)।
অর্থাৎ ‘সবিতা নানা যন্ত্রের দ্বারা পৃথিবীকে সুস্থির রেখেছেন তিনি বিনা খুঁটিতে আকাশকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করেছেন।
উপরের শ্লোকটি একটি বিশেষ কারণে আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। এটি থেকে বোঝা যায়, বৈদিক যুগে মানুষেরা পৃথিবীকে তো স্থির ভাবতেনই, আকাশকে ভাবতেন পৃথিবীর ছাদ। তারা ভাবতেন ঈশ্বরের অপার মহিমায় এই খুঁটি বিহীন ছাদ আমাদের মাথার ওপরে ঝুলে রয়েছে। কোরআনের সুরা লুকমানে (৩১ : ১০) বর্ণনা আছে এইভাবে–
‘তিনিই খুঁটি ছাড়া আকাশকে ছাদ স্বরূপ ধরে রেখেছেন কিন্তু আজ এই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যুগে আমরা জানি, আকাশ কখনোই পৃথিবীর ছাদ নয়। সত্যিকার অর্থে তো আকাশ বলেই কিছু নেই। আকাশ হচ্ছে আমাদের দৃষ্টির প্রান্তসীমা। পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডল থাকার কারণে আমাদের চোখে আকাশকে নীল দেখায়। চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই, তাই চাঁদের আকাশ কালো। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে যে, ‘মহাবিজ্ঞানময়’ কিতাবগুলোতেও এধরনের কোনো বিজ্ঞানভিত্তিক সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির সন্ধান পাওয়া যায় না। মানুষ কবে বড় হবে? ধর্মগ্রন্থগুলো থেকে মুখ সরিয়ে কবে সত্যি সত্যিই একদিন বুঝতে শিখবে ‘আকাশ’ শব্দটার মানে? সুনীলের কবিতার একটা গাছ তলায় দাঁডিযে’ কবিতার কয়েকটি লাইন এ প্রসঙ্গে খুবই অর্থবহ–
… এতগুলো শতাব্দী গড়িয়ে গেল, মানুষ তবু ছেলেমানুষ
রয়ে গেল
কিছুতেই বড় হতে চায় না
এখনও বুঝলো না ‘আকাশ’ শব্দটার মানে
চট্টগ্রাম বা বাঁকুড়া জেলার আকাশ নয়
মানুষ শব্দটাতে কোনো কাঁটাতারের বেড়া নেই
ঈশ্বর নামে কোনো বড় বাবু এই বিশ্ব সংসার চালাচ্ছেন না।
ধর্মগুলো সব রূপকথা
যারা এই রূপকথায় বিভোর হয়ে থাকে
তারা প্রতিবেশীর উঠোনের ধুলোমাখা শিশুটির কান্না শুনতে
পায় না
তারা গর্জন বিলাসী ..
.
সমতল পৃথিবী
আমার নিবন্ধটি সেই অনলাইন পত্রিকাটিসহ অন্যান্য জায়গায় প্রকাশের পর বেশ কিছু প্রতিক্রিয়া হয়। আমার এক ধার্মিক বান্ধবী ই-মেইলে জানায়, ‘হতে পারে কোরআনে কোথাও বলা নাই যে পৃথিবী ঘুরছে। কোরআনে তো কতকিছুই সোজাসুজি বলা নাই। যেমন, কোরআনে তো এ কথাও বলা নাই যে পৃথিবী গোলাকার। কিন্তু তার মানে তো এই নয় যে কোরআনের দৃষ্টিতে পৃথিবী সমতল।”
উত্তরে আমি জানালাম, কোরআনের দৃষ্টিতে পৃথিবী সত্যিই সমতল! নিম্নোক্ত এই সুরাগুলো তার প্রমাণ–
.. পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি (কার্পেটের মতো) এবং ওতে পর্বতমালা সৃষ্টি করেছি …’ (১৫ : ১৯)
‘যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে (সমতল) শয্যা করেছেন এবং ওতে তোমাদের জন্য চলার পথ দিয়েছেন … (২০ : ৫৩, যুখরুখ ৪৩ : ১০)
‘ আমি বিস্তৃত করেছি (কার্পেটের মতো) পৃথিবীকে এবং ওতে পর্বত মালা স্থাপন করেছি … (৫০ : ৭)
‘আমি ভূমিকে বিছিযেছি, আর তা কত সুন্দরভাবে বিছিযেছি …’ (৫২ : ৪৪)।
‘আল্লাহ তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত … (৭১ : ১৯) ইত্যাদি।
উপরের আয়াতগুলো থেকে বোঝা যায়, পদার্থবিদরা যেভাবে আজ গোলাকার পৃথিবীর ধারণা পোষণ করেন, কোরআনের পৃথিবী তার সাথে মোটেও সংগতিপূর্ণ নয়। সমতলভাবে বিস্তৃত পৃথিবীর কথা বোঝানোর জন্য যত রকমের শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে তার প্রায় সবই। কোরআনে ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দগুলো হচ্ছে ফিরাশা, মাদ্দা, মাদাদনা, মান্দা, মাদাদনাহা, ফারাশনা, আল-মাহিদুন, বিতা, মিহাদা, দাহাহা[২২৭], সুতিহাত এবং তাহাহা। একই ধরনের শব্দ বিভিন্ন পদে ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলো সবই সমতল পৃথিবীর স্বরূপকেই তুলে ধরে[২২৮]। আমি এই প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত সুরা কাহাফ (১৮ : ৮৬) এর প্রতি আবারও পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যেখানে বলা আছে আল্লাহর এক বিশ্বস্ত বান্দা কাদামাটি পূর্ণ একটি নির্দিষ্ট স্থানে সূর্যকে ডুবতে দেখেছিলেন। একই সুরার ৯০ নং আযাতে একটি নির্দিষ্ট স্থান হতে সূর্যোদয়েরও বর্ণনা আছে। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে আল্লাহ কেন ভাবলেন যে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান দরকার? এর মধ্য থেকে একটি সত্যিই বেরিয়ে আসে, আর তা হলো কোরআনের গ্রন্থাকার পৃথিবীকে গোলাকার ভাবেন নি, ভেবেছেন সমতল।
নামাজ পড়ার নির্দিষ্ট সময়ের কথা মাথায় রাখলে পরিষ্কার বোঝা যায় প্রাচীনকালে মানুষের মতো আল্লাহও সমতল পৃথিবীর ধারণা থেকে একদমই বেরুতে পারেন। নি। আমাদের বাঙালি কৃষক-দার্শনিক আরজ আলী মাতুব্বর তার ‘সত্যের সন্ধান’ বইতে চমৎকারভাবে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছেন। এই সুযোগে সেটা আবার একটু ঝালিয়ে নেওয়া যাক। ইসলামি শাস্ত্রে প্রত্যেকদিন পাঁচবার নামাজ পড়ার বিধান আছে। এই পাঁচবারের জন্য নির্দিষ্ট সময় বরাদ্দ আছে, আবার কোনো কোনো সময়ে নামাজ পড়া আবার নিষিদ্ধ। যেমন, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত অথবা মধ্যাহ্নে নামাজ পড়ার কোনো নিয়ম নেই। কিন্তু পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে আমরা জানি যেকোনো স্থির মুহূর্তে বিভিন্ন দ্রাঘিমার ওপর বিভিন্ন সময় দেখা দেয় এবং প্রতিমুহূর্তেই পৃথিবীর কোনো না কোনো স্থানে নির্দিষ্ট উপাসনা চলতে থাকে। এর মানে কী? যেমন ধরা যাক, বরিশালে যখন সূর্যোদয় হচ্ছে, তখনও কলকাতায় সূর্য ওঠে নি আর চট্টগ্রামে কিছুক্ষণ আগেই সূর্য উঠে গেছে। কাজেই বরিশালে যখন ইসলামের দৃষ্টিতে নামাজ পড়া হারাম, তখন কলকাতা বা চট্টগ্রামে তা হারাম নয়। তা হলে নির্দিষ্ট সময়ে উপাসনা নিষিদ্ধ করার কোনো মানে আছে? যুক্তিবাদী আরজ আলী ‘সত্যের সন্ধানে’ বইতে একটি মজার প্রশ্ন করেছেন। ধরা যাক, একজন লোক বেলা দেড়টায় জোহরের নামাজ পড়ে বিমানে চড়ে মক্কায় যাত্রা করলেন। সেখানে পৌঁছে তিনি দেখলেন যে ওখানে তখনও দুপুর হয় নি। ওখানে জোহরের ওয়াক্তের সময় হলে কি তার আরেকবার জোহরের নামাজ পড়তে হবে? আপাত নিরীহ এই প্রশ্নটির মধ্যেই কিন্তু উত্তরটি লুকিয়ে আছে আরজ আলী নিজেই এর উত্তর দিয়েছেন–
এক সময় পৃথিবীকে স্থির আর সমতল মনে করা হতো। তাই পৃথিবীর সকল দেশে বা সকল জায়গায় একই রকম সময় সূচিত হবে, বোধহয় এইরকম ধারণা থেকে ওই সমস্ত নিয়ম-কানুন প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু এখন প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবী গোল ও গতিশীল।
আসলে আধুনিক জীবনযাত্রার সাথে তাল মেলাতে পুরনো ধর্মীয় কানুন মানতে গিয়ে দেখা দিচ্ছে নানা জটিলতা। ভবিষ্যতে এই জটিলতা আরও বাড়বে। যেমন, কোনো নভোচারী অথবা কোনো বিমান চালক ১০৪১.৬৭ মাইল বেগে পশ্চিম দিকে বিমান চালালে সূর্যকে সবসময়ই তার কাছে গতিহীন বলে মনে হবে। অর্থাৎ বিমান আরোহীদের কাছে সকাল, দুপুর আর সন্ধ্যা বলে কিছু থাকবে না। সূর্য যেন স্থিরভাবে একস্থানে দাঁড়িয়ে থাকবে। এই অবস্থায় বিমান আরোহীদের নামাজ-রোজার উপায় কী? ভবিষ্যতে মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি যদি বসতি গড়তে হয়, তবে দেখা দেবে আরও এক সমস্যা। সেখানে প্রায় ছয় মাস থাকে দিন আর ছয় মাস থাকে রাত। সেখানে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা রাখা আর দিনে পাঁচ বার নামাজ পড়া কি আদৌ সম্ভব? এটি বোঝা মোটেই কঠিন নয় যে, প্রাচীনকালে মানুষের সমতল পৃথিবী ব্যাপারে ভুল ধারণার কারণেই আজকের দিনে নিয়ম পালনে এই জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।
ইতিহাসের পাতায় এবার চোখ রাখা যাক। এগারো শতকের বিখ্যাত আরবীয় বিজ্ঞানী ইবন-আল হাইয়াম ধারণা করেছিলেন যে পৃথিবী সমতল নয়, বরং গোলাকার। তার সমস্ত কাজ সেসময় ধর্মবিরোধী বলে বাজেয়াপ্ত করা হয়, আর তার সমস্ত বইও পুড়িয়ে দেওয়া হয়[২২৯]। ১৯৯৩ সালে, সৌদি আরবের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা শেখ আবদেল আজিজ ইবন বাজ এই বলে একটি ফতোয়া জারি করেন–
এই পৃথিবী সমতল। যারা এই সত্যটা মানে না তারা সকলেই নাস্তিক, শাস্তিই তাদের কাম্য।
কার্ল স্যাগানের ‘The Demon-Haunted World’ বইয়ে এই বিখ্যাত ফতোয়ার উল্লেখ পাওয়া যাবে[২৩০]।
হিন্দু পুরাণগুলোর অবস্থাও তথৈবচ। নরসিংহ পুরাণের ১৬৯ পৃষ্ঠায় সমতল পৃথিবীর পরিষ্কার বর্ণনা আছে। তাই গুজরাটে বারোদায় ‘জাম্বুদ্ভিপা’ নামের একটি প্রতিষ্ঠান এখনও বৈদিক সমতল পৃথিবীকে ‘বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করার প্রাণান্তকর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।
১৯৯৯ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর কেনসাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টিম মিলার দাবি করলেন যে, ‘বাইবেল অনুযায়ী, পৃথিবীর চারটি প্রান্ত আছে।’ এবং তিনি আরও দাবি করলেন যে, তিনি বিশ্বাস করেন পৃথিবী আসলে হয় চতুর্ভুজ আকৃতির অথবা আয়তাকার। আসলে কোরআন, বাইবেল আর বেদের মতো ধর্মগ্রন্থে লেখা ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে কিছু মানুষ এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়েও মনে করে পৃথিবী গোলাকার নয়, সমতল। তারা আন্তর্জাতিক সমতল পৃথিবী সমিতি (International Flat Earth Society[২৩১]) এবং ‘আন্তর্জাতিক চতুর্ভুজাকার পৃথিবী সমিতি (The International Square Earth Society[২৩২]) এধরনের হাস্যকর সমস্ত নামে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তুলেছে যাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে পৃথিবীবাসীকে বোঝানো যে, বিজ্ঞান যাই বলুক না কেন, পৃথিবী কিন্তু সমতল!
.
ভুল করে ভুল করা
তথ্যগত ভুল কিংবা প্রাচীন চিন্তাধারার নিদর্শন রয়েছে কোরআন শরীফে ভ্রান্ত ‘সমতল এবং অনড়’ পৃথিবীর ধারণাই কেবল নয়, এখানে আছে অদৃশ্য ‘শয়তান জ্বীন’ এর উপস্থিতির উল্লেখ (৬ : ১০০, ৬ : ১১২, ৬ : ১২৮, ৬ : ১৩০, ৭ : ৩৮, ১১ : ১১৯, ১৫ : ২৭। ইত্যাদি), যাদের কাজ হচ্ছে একজনের ওপর আরেকজন দাঁড়িয়ে ‘Exalted Assembly’ তৈরি করা (৩৭ : ০৪) আর কানাকানি করে গোপন কথা শুনে ফেলা (৭২ : ৪, ৩৭ : ৬/১০)। আকাশে আমরা উল্কাপাত ঘটতে দেখি কারণ এই অদৃশ্য শয়তান এবং জ্বীনদের ভয় দেখানোর জন্যই আল্লাহ এমনটা ঘটান (৭২ : ৯, ৩১ : ১০)। কীভাবে জুলকারনাইন এক পঙ্কিল জলাশযে’ সূর্যকে ডুবতে দেখেছেন, তার উল্লেখ যে কোরআনে আছে, তা তো এ অধ্যায়ের আগেই বলেছি। এধরনের ভুল আরও আছে। যেমন, বলা আছে শুক্রাণু তৈরি হয় মেরুদণ্ড এবং পাঁজরের মধ্যবর্তী জায়গা থেকে (৫৬ : ৬-৭); মাতা মেরিকে বর্ণনা করা হয়েছে অ্যারনের (মুসার বড় ভাই) বোন হিসেবে (১৯ : ২৮)। এগুলো সঠিক নয়। আর হাদিসে বলা হয়েছে যে, যখন কোনো পুরুষের শুক্রাণু কোনো মহিলার জরায়ুতে প্রবেশ করে, তখন আল্লাহ কর্তৃক নিযুক্ত ফেরেশতারা তার দায়িত্ব নিয়ে নেয় (সহি বোখারী ১.৬.৩১৫, ৪.৫৪ . ৪৩০; সহি মুসলিম ৩৩.৬৩৯২ ইত্যাদি), মানুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো ইসলামি পাপ বয়ে নিয়ে যায়’ (সুনান নাসাই ১.১৪৯), এমনকি কোরআন-হাদিস অনুযায়ী মানব অঙ্গগুলো কথা পর্যন্ত বলতে পারে (কোরআন ৪১ : ২০, ৪১ : ২১, ৩৬ : ৬৫, ২৪ : ২৪)। তাও না হয়। মানা গেল, কিন্তু হাদিসে উটের মূত্রকে যে রোগনাশকারী মহৌষধ হিসেবে বর্ণনা করে তা নিয়মিতভাবে পান করার পরামর্শ যে দেওয়া হয়েছে, তা কি আমরা জানি? যেমন, সহি বোখারীর ভলিউম ৭, বই ৭১, হাদিস নং ৫৯০ দেখা যাক–
আনাস (রা.) হতে বর্ণিত : কিছু লোকের মদিনার আবহাওয়া প্রতিকূল মনে হচ্ছিল। রাসুল (সা.) তাদেরকে নির্দেশ দিলেন উটের রাখালের সাথে বাস করতে এবং উটের দুধ ও মূত্র থেতে (ঔষধ হিসেবে)। তারা রাখালের সাথে থাকতে লাগলো এবং উটের দুগ্ধ এবং মূত্র পান করতে লাগলো যতদিন পর্যন্ত তারা সুস্থ হয়ে ওঠে। এরপর তারা রাখালকে মেরে তার উট নিয়ে পালাতে লাগলো। খবর পেয়ে রাসুল (সা.) তাদেরকে ধরে আনতে বললেন। তাদেরকে রাসুলের সামনে উপস্থাপন করার পর তিনি তাদের হাত পা কেটে এবং চোখে লৌহ তপ্ত শলাকা ঢুকিয়ে হত্যা করার আদেশ দিলেন।
উটের দুধের পাশাপাশি মূত্র পানের উপকারিতার কথা বলা আছে আরও অনেক হাদিসেই, এবং ইবনে ইসহাকের সিরাতেও[২৩৩]।
কোরআনের কয়েকটি আয়াত থেকে পাওয়া যায়, এই মহাবিশ্ব তৈরি করতে আল্লাহ সময় নিয়েছেন ছয় দিন (৭ : ৫৪, ১০ : ৩, ১১ : ৭, ৫০ : ৩৮, ৫৭। : ৪ ইত্যাদি), কিন্তু ৪১ : ৯-১২ থেকে জানা যায়, তিনি পৃথিবী তৈরি করতে ২ দিন সময় নিয়েছিলেন, এরপর এর মধ্যে পাহাড়-পর্বত বসাতে আর অন্যান্য আনুষঙ্গিক ইমারত তৈরি করতে আরও চার দিন, সবশেষে সাত আসমান বানাতে সময় নিয়েছেন আরও দু-দিন। সব মিলিয়ে সময় লেগেছে মোট আট দিন। কাজেই কোরআন অনুযায়ী আল্লাহ মহাবিশ্ব বানিয়েছেন কয় দিনে-ছয় দিনে নাকি আট দিনে? সুরা ৭৯ : ২৭ ৩০ অনুযায়ী আল্লাহ বেহেশত’ বানিয়েছিলেন আগে, তারপর বানিয়েছিলেন পৃথিবী, কিন্তু অন্য কিছু আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, আগে পৃথিবী পরে বেহেশত (২ : ২৯ এবং ৪১ : ৯-১২ দ্র.)। কখনও বলা হয়েছে আল্লাহ সবকিছু ক্ষমা করে দেন (৪ : ১১০, ৩৯ : ১৫৩) কিন্তু আবার অন্যত্র বলা হয়েছে, তিনি সবকিছু ক্ষমা করেন না (৪ : ৪৮, ৪ : ১১৬, ৪: ১৩৭, ৪ : ১৬৮)। সুরা ৩ : ৮৫ এবং ৫ : ৭২ অনুযায়ী ইসলাম ধর্মে যারা নিজেদের সমর্পণ করে নি তারা। সবাই দোজখে যাবে তা সে খ্রিস্টান, ইহুদি, প্যাগান যেই হোক না কেন, কিন্তু আবার ২ : ৬২ এবং ৫ : ৬৯ অনুযায়ী, ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের সবাই দোজখে যাবে না। কখনও বলা হয়েছে মুহাম্মদকে সাহায্যের জন্য প্রস্তুত আছেন এক হাজার জন ফেরেশতা (৮ : ৯-১০) কখনোবা বলেছেন এই সাহায্যকারী ফেরেশতাদের সংখ্যা আসলে তিন হাজার (৩ : ১২৪, ১২৬)। কথনও আল্লাহ বলেছেন তার একটি দিন পার্থিব এক হাজার বছরের সমান (২২ : ৪৭, ৩২ : ৫), কখনোবা বলেছেন, তার দিন পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান (৭০ : ৪)। মানব সৃষ্টি নিয়েও আছে পরস্পর-বিরোধী তথ্য। আল্লাহ কোরআনে কখনও বলেছেন তিনি মানুষ বানিয়েছেন পানি থেকে (২৫ : ৫৪, ২৪ : ৪৫), কখনোবা জমাট রক্ত বা ‘ক্লট’ থেকে (৯৬: ১-২), কখনোবা কাদামাটি থেকে (১৫ : ২৬, ৩২: ৭, ৩৮ : ৭১, ৫৫ : ১৪) আবার কখনোবা ‘ডাস্ট বা ধূলা থেকে (৩০ : ২০, ৩৫ : ১১) ইত্যাদি। একই সাথে এত ধরনের পরস্পরবিরোধী তথ্য ঠিক কোন ঐশী অর্থ প্রকাশ করে?
.
পৌরাণিক বিগব্যাং
আবারও ফিরে আসি বিজ্ঞানময় কিতাবের জগতে। ফিরে আসতেই হয় বারে বারে-বুকাইলি, হারুন ইয়াহিয়া আর মুরদের কল্যাণে। সোজা হয়ে প্রশ্নটার মুখোমুখি দাঁড়াতেই হয় অবশেষে-’সত্যিই কি কোরআন অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত আর মহা-বিজ্ঞানময় এক নিখুঁত ঐশী কিতাব?’ বব ডিলানের বাংলা করে কবীর সুমন যেভাবে গেযেছে, সেভাবেই বলি-’প্রশ্নগুলো সহজ, আর উত্তরও তো জানা’। উত্তর হচ্ছে-মোটেই কোরআন অলৌকিক কোনো গ্রন্থ নয়। কোরআনে আসলে কোথাও বিগব্যাং-এর কথা নেই, রিলেটিভিটির কথা নেই, কৃষ্ণগহ্বরের কথা নেই, অণু-পরমাণুর কথাও নেই। বিগব্যাং আর রিলেটিভিটির নামে যা দেখা যায়, তা হলো আদিম সুরাগুলোর ‘আধুনিক এবং চতুর’ ব্যাখ্যা। নিচের উদাহরণটি দেখা যাক–
অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না, আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম (২১ : ৩০)
‘কিতাব-বিশেষজ্ঞ’-এর দল এই আয়াতটির মধ্যে বিগব্যাং-এর গন্ধ খুঁজে পান। কিন্তু আসলেই কি এর মধ্যে বিগব্যাং-এর কোনো আলামত আছে? একটু যৌক্তিক মন নিয়ে আলোচনা করা যাক। এই আয়াত এবং তার পরবর্তী আয়াতগুলোর দিকে তাকানো যাক
‘আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম’ (২১ : ৩০)।
এবং আমি এ জন্য পৃথিবীতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি, যেন তা সহ এটি না নড়ে’ (২১ : ৩১)।
‘এবং আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ’ (২১ : ৩২)।
‘আল্লাহই উপ্ন দেশে স্তম্ভ ছাড়া আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছেন’ (১৩ : ২)।
এই আয়াতগুলো আমাদের আকাশ আর পৃথিবীর মধ্যকার সম্পর্ক বিষযে আসলে খুব প্রাচীন আর অস্পষ্ট একটি ধারণা দেয়। আল্লাহ আকাশকে ‘স্তম্ভ বিহীন’ ছাদ হিসেবে স্থাপন করার পর পৃথিবীতে পর্বতমালা স্থাপন করলেন যাতে কিনা আমাদের এ পৃথিবী না নড়ে, ঠিক যেমনটি আমরা পাতলা কোনো কাগজ বাতাসে উড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ওটাকে পেপার ওযেট দিয়ে চাপা দেই। আল্লাহ মানুষের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কী করলেন? আকাশকে অদৃশ্য খুঁটির ওপর বসিয়ে দিলেন। এগুলো কী করে বিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলামত হয়? আর সবচেয়ে বড় কথা, ‘আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এই আয়াতটি যদি মহা-বিস্ফোরণের (বিগব্যাং) প্রমাণ হয়, তবে কোথায় এখানে বিস্ফোরণের উল্লেখ? ‘বিগব্যাং’ শব্দটি নিজেই এখানে তাৎপর্যবাহী। এই আয়াতের কোথায় রয়েছে সেই বিখ্যাত ব্যাঙ’ (বিস্ফোরণ)–এর ইঙ্গিত?
উপরন্ত, পদার্থবিজ্ঞানে ‘বিগব্যাং’ স্থান-কাল অদ্বিতীয়ত্বের (space-time singularity) সাথে জড়িত, পদার্থের সাথে নয়। বিগব্যাং-এর প্রক্রিয়া যখন শুরু হয়েছিল তখন পৃথিবীর অস্তিত্বই ছিল না, পৃথিবীর জন্ম হয়েছে বিগব্যাং-এর সাড়ে নয়শ কোটি বছর পরে উপরের আয়াতটি শুধু আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে থাকার (বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে যার কোনো অর্থই হয় না) কথাই বলছে আর পরে বলছে উভয়কে পৃথক করে’ (বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আবারও যার কোনো অর্থ নেই) দেওয়ার কথা যা বৈজ্ঞানিক বক্তব্য হতে পারে না, বিগব্যাং তো অনেক পরের কথা।
কতগুলো অর্থহীন শব্দমালা ‘আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল, পরে আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম’ কখনোই বৈজ্ঞানিকভাবে বিগব্যাং’কে প্রকাশ করে না[২৩৪]। কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞান থেকে আমরা জানি, মহাবিস্ফোরণ-মুহূর্তে প্রকৃতির চারটি বল-শক্তিশালী নিউক্লিয় বল, দুর্বল নিউক্লিয় বল, তড়িৎ-চুম্বকীয় বল আর মাধ্যাকর্ষণ বল ‘একীভূত শক্তি’ (super force) হিসেবে প্রকৃতিতে বিদ্যমান ছিল। উপরের আয়াতটিতে কোথায় তার ইঙ্গিত? কীভাবে একজন ওই আয়াতটি থেকে হাবলের ধ্রুবক বের করতে পারবে? কীভাবে মাপতে পারবে ডপলারের বিচ্যুতি? উত্তর নেই।
জ্যোতিপদার্থবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণার দিকে খানিকটা চোখ বুলানো যাক। অ্যালেন গুথ এবং আঁদ্রে লিন্ডের সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে পাওয়া ফলাফল থেকে জানা গিয়েছে, আমাদের মহাবিশ্ব যদি কোয়ান্টাম ফ্লাকচুযেশনের মধ্য দিয়ে স্থান-কালের শূন্যতার ভিতর দিয়ে আবির্ভূত হয়ে থাকে, তবে এ পুরো প্রক্রিয়াটি কিন্তু একাধিকবার ঘটতে পারে, এবং হয়ত বাস্তবে ঘটেছেও। ব্যাপারটিকে বলে মাল্টিভার্স বা ‘অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণা[২৩৫]। এ ধারণায় মনে করা হয়, কেওটিক ইনফ্লেশনের মাধ্যমে সম্প্রসারিত বুদ্বুদ (Expanding Bubbles) থেকে আমাদের মহাবিশ্বের মতোই অসংখ্য মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে, যেগুলো একটা অপরটা থেকে সংস্পর্শবিহীন অবস্থায় দূরে সরে গেছে। এধরনের অসংখ্য মহাবিশ্বের একটিতেই হয়ত আমরা অবস্থান করছি (পকেট মহাবিশ্ব) অন্যগুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে একেবারেই জ্ঞাত না হয়ে।
কাজেই, বিজ্ঞানের চোখে বিগব্যাংই শেষ কথা নয়। বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক গবেষণাগুলো বিগব্যাং-এর আগে কী ছিল তারও একটি সার্বিক উত্তর খুঁজতে সচেষ্ট হয়েছে। আসলে ইনফ্লেশন বা স্ফীতি নিয়ে আঁদ্রে লিন্ডে আর তার দলবলের সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে সত্যিকার অর্থেই সেই উত্তপ্ত বিগব্যাং’ যার মধ্য দিয়ে এ মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়, তাকে বিদায় জানানোর সময় এসে গিয়েছে। কারণ, সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, বিগব্যাং দিয়ে মহাবিশ্বের শুরু নয়, বরং মহাবিশ্বের শুরু হয়েছে ইনফ্লেশন দিয়ে। অর্থাৎ, বিগব্যাং-এর পরে ইনফ্লেশনের মাধ্যমে মহাবিশ্ব তৈরি (যা কিছুদিন আগেও সত্যি বলে ভাবা হতো) হয় নি, বরং ইনফ্লেশনের ফলেই কিন্তু বিগব্যাং হয়েছে, তারপর সৃষ্টি হয়েছে আমাদের মহাবিশ্ব। আঁদ্রে লিন্ডের কথায়[২৩৬]–
১৫ বছর আগেও আমরা ভাবতাম ইনফ্লেশন হচ্ছে বিগব্যাং-এর অংশ। এখন দেখা যাচ্ছে বিগব্যাং-ই বরং ইনফ্লেশনারি মডেলের অংশবিশেষ।
এখন কথা হচ্ছে, বিগব্যাং-এর মডেল কখনও ভুল প্রমাণিত হলে কিংবা পরিবর্তিত/পরিশোধিত হলে কী হবে? সাথে সাথে কি ধার্মিকেরাও বিগব্যাং-এর সাথে ‘সংগতিপূর্ণ আয়াতকে বদলে ফেলবেন? তাহলে তখন ‘আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে ছিল’-এই আপ্তবাক্যের কী হবে? এই ধরনের আশঙ্কা থেকেই কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন বিশ্বাসী পদার্থবিজ্ঞানী আব্দুস সালাম জ্যোতির্পদার্থবিজ্ঞানের বিগব্যাং তত্বকে কোরআনের আয়াতের সাথে মেশাতে বারণ করতেন। তিনি বলতেন[২৩৭]–
বিগব্যাং তত্বের সাম্প্রতিক ভাষ্যটি বর্তমানে মহাবিশ্বের উৎপত্তির সর্বোৎকৃষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করছে। কিন্তু আগামীকাল যদি এর চাইতেও কোনো ভালো ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাহলে কী হবে? তাহলে কি নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সাথে তাল মেলাতে গিয়ে ধর্মগ্রন্থের আয়াত বদলে ফেলা হবে?
খুবই যৌক্তিক শঙ্কা। ঠিক একই কারণে ১৯৫১ সালে যখন Pope Pius XII বাইবেলের সৃষ্টিতত্বের সাথে বিগব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্বের মিল খুঁজে পেলেন, তখন জ্যোর্তিবিজ্ঞানী এবং খ্রিস্টান ধর্মযাজক জর্জ হেনরি লেমিত্রি (যিনি ‘বিগব্যাং’ প্রতিভাসের একজন অন্যতম প্রবক্তা) পোপকে বিনয়ের সঙ্গে এধরনের যুক্তিকে ‘অভ্রান্ত হিসেবে প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই পরামর্শ মানছে কে?
.
মিরাকল নাইন্টিন
প্রার্থনা করে এমন ঠোঁটের চেয়ে একটি কর্মঠ হাত অনেক বেশি উত্তম। ধর্ম এবং বিজ্ঞান দুটি একেবারে দু মেরুর বস্তু হলেও মানুষ আজ একটি জিনিস বুঝতে পেরেছে, বিজ্ঞান আসলে কাজ করে, ফল দেয়। অন্যদিকে, পদে পদে ধর্মের অসাড়তা তারা অনুবাধন করতে পারলেও পরকালের লোভে পড়ে কেউই অবশ্য সেটাকে নিজের মনে জায়গা দিতে চান না। অস্তিত্ব টিকিযে রাখার লোভে ধর্ম আজ তাই নতুন এক খোলসে নিজেদের গা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করছে। নিজেদের বিজ্ঞানময় প্রমাণ করে টিকিয়ে রাখতে চাচ্ছে বিজ্ঞানের যুগে। আর তা করতে গিয়ে সৃষ্টি করেছে মিথ্যা, চালাকির এক প্রশান্ত মহাসাগরের উপরে তেমন কিছু উদাহরণ নিয়ে আলোচনা হলো। এখন দৃষ্টিপাত করা যাক একেবারে ভিন্ন একটি ব্যাপারের দিকে।
কোরআনে কেবল বিজ্ঞানময় কথাবার্তা নয়, নিজের শ্রেষ্ঠত্বের নমুনা মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য স্রষ্টা তার লিখিত এ গ্রন্থে এক অলৌকিক ব্যাপার রেখে দিয়েছেন-তিনি কোরআনকে বেঁধে দিয়েছেন উনিশ সংখ্যা দ্বারা। অলৌকিক এ বিষয়টি অবশ্য মুসলিমদের অজানাই থেকে যেত যদি না এ শতকেই বিষয়টি প্রথমবারের মতো জনসমক্ষে তুলে না ধরতেন রাশাদ খলিফা নামের এক ভদ্রলোক[২৩৮]। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে। রাশাদ খলিফা মুসলিম বিশ্বে হইচই ফেলে দেন। বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন দেশে শ’থানের বেশি বই রচিত হয় বিষয়টি নিয়ে। বাংলাদেশে মেজর কাজী জাহান মিয়া লিখিত ‘আল-কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ’ নামক বইটির প্রথম চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে এই ১৯ মিরাকল[২৩৯]। ড. খন্দকার আব্দুল মান্নান লিখিত কম্পিউটার ও আল কোরআন’ নামক বইটিতে স্থান পেয়েছে ১৯-এর চমৎকারিত্ব[২৪০]। আল কোরআন অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ আরও এক ধাপ এগিয়ে। কোরআনের বাংলা অনুবাদ করার পর প্রথমেই তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে রাশাদ খলিফার উনিশের ম্যাজিকের কথা তুলে ধরেন[২৪১]। কী তবে সেই উনিশের ম্যাজিক?
সুরা আল-মুদাচ্ছিরের ৩০ নম্বর আয়াতে আল্লাহ বলেন, ‘ইহার ওপর আছে উনিশ। এর আগে পরে কী উল্লেখ আছে, কার ওপরে উনিশ আছে এমন সকল প্রশ্নকে পাশ কাটিযে খলিফা অপ্রাসঙ্গিকভাবে শুধু আয়াতটি তুলে এনে দাবি করেন, এর মাধ্যমে আল্লাহ কোরআনকে উনিশ দিয়ে বেধে রাখার কথা উল্লেখ করেছেন। দাবিকে যৌক্তিক প্রমাণের জন্য তিনি কিছু উদাহরণ হাজির করেন। যেমন : কোরআনের সুরা সংখ্যা ১১৪ যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য। কোরআনের আয়াত সংখ্যা ৬৩৪৬, যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য (১৯ x ৩৩৪ = ৬৩৪৬) এবং এ সংখ্যাটির অঙ্কগুলোর যোগফল ১৯ (৬ + ৩ + ৪ + ৬ = ১৯), কোরআনে ‘বিসমিল্লাহ ১১৪ বার এসেছে যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য হয়। এছাড়া ‘বিসমিল্লাহ’-তে ১৯টি বর্ণ রয়েছে, কোরআনের সর্বমোট বর্ণসংখ্যা ৩২৯১৫৬, যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য (১৯ x ১৭৩২৪ = ৩২৯১৫৬), কোরআনে ‘আল্লাহ’ শব্দটি ২৬৯৮ বার উল্লেখিত হয়েছে যা ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য (১৯ x ১৪২ = ২৬৯৪)।
এছাডা ‘আল্লাহ’ উল্লেখ আছে এমন আয়াতগুলোর আয়াত নম্বর যোগ করলে যোগফল হয় ১১৮১২৩, যা ১৯ দিয়ে। নিঃশেষে বিভাজ্য (১৯ x ৬২১৭ = ১১৮১২৩) ইত্যাদি ইত্যাদি। রাশাদ খলিফার প্রদানকৃত পুরো গাণিতিক হিসাবটি যেকোনো মানুষকে আকৃষ্ট করবে। যিনি ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী তিনি প্রমাণটি দেখে তৃপ্তির ঢেকুর তুলবেন জিনিসটা মাথায় রাখার চেষ্টা করবেন, ক্ষেত্র বিশেষে কোনো সংশয়বাদীর সাথে তর্কে লিপ্ত হলে তলোয়ার হিসেবে ব্যবহার করবেন। আর যিনি অবিশ্বাসী তিনিও সামান্য দ্বন্দ্বে পড়ে যাবেন।
অলৌকিক কোরআন নিয়ে আলোচনায় যাওয়ার আগে সামান্য একটু জল ঘোলা করা যাক! সেই পিথাগোরাসের আমল থেকে শুরু হওয়া সংখ্যা নিয়ে এধরনের ধাঁধাময় খেলার ইতিহাস অনেক প্রাচীন। Numerology তথা সংখ্যাতত্ব হিসেবে পরিচিত বিষয়টি আধুনিক বিজ্ঞান জন্মলগ্নেই গণিত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গিযেছে; যেমনটি জ্যোতিষশাস্ত্র আলাদা হয়েছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান থেকে, আলকেমি আলাদা হয়েছে রসায়ন থেকে। বিজ্ঞানের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অপব্যবহারকেই অপবিজ্ঞান আখ্যায়িত করা হয়। সংখ্যাতত্ব একটি অপরিপূর্ণ গণিত বা অপবিজ্ঞান সংখ্যাতত্ত্বের উদাহরণ অজস্র। সেই মধ্যযুগ থেকে সংখ্যাতত্বে মত্ত ইহুদিরা সেসময়ই তাদের ধর্মগ্রন্থ তোরাহ-র দ্বিতীয় গ্রন্থ এক্সোডাস থেকে স্রষ্টার রহস্যময় নাম বের করেছিল। এক্সোডাসের ১৪ : ১৯-২১, এই তিনটি আয়াতের মাধ্যমে তারা স্রষ্টার ৭২টি নাম উদ্ভাবন করেছে। এই প্রতিটি আয়াতে ৭২টি করে বর্ণ আছে। প্রথমে তারা প্রথম আয়াতটি ডান থেকে বামে লিখে তারপর দ্বিতীয় আয়াত বাম থেকে ডানে লিখেছে। সবশেষে তৃতীয় আয়াতটিকে আবার ডান থেকে বামে লেখার মাধ্যমে। সম্পূর্ণ কাজটিকে তারা ১৮টি কলাম এবং ১২ সারিতে ভাগ করা হয়েছে। ১৮ গুণ ১২ = ৭২ গুণ ও এই সুত্র ধরে তারা ১২টি সারিকে ৩ সারি ৩ সারি করে ভাগ করেছে। মোট চারটি ভাগ হয়েছে যার প্রতিটিতে ১৪ কলাম ও ৩ সারি। প্রতি ভাগের একটি কলাম দ্বারা স্রষ্টার একটি তিন অক্ষরের নাম পাওয়া গেছে। এভাবে মোট ১৮ গুণ ৪ = ৭২ টি তিন অক্ষরের নাম পাওয়া। গেছে। চার ভাগের প্রতিটিকে আবার আরেকটি বর্ণের সাথে মেলানোর মাধ্যমে স্রষ্টার চার অক্ষরের একটি নাম পাওয়া গেছে[২৪২]।
আজ অবধি সেই চার অক্ষরের নামটির ও তার সঠিক উচ্চারণ জানার চেষ্টা করছে তারা। আরও মজা পাওয়া যাবে যুক্তরাষ্ট্রে সংগঠিত নাইন ইলেভেনের বিমান হামলার ঘটনার সংখ্যাতত্ত্ব নিয়ে হামলার তারিখ ৯/১১ : ৯ + ১ + ১ = ১১; ১১ই সেপ্টেম্বর বছরের ২৫৪তম দিন : ২ + ৫ + ৪ = ১১; ১১ই সেপ্টেম্বর পর বছর শেষ হতে ১১১ দিন বাকি থাকে; ১১৯ হচ্ছে ইরাক/ইরানের রাষ্ট্রীয় কোড ১ + ১ + ৯ = ১১; ইংরেজি ‘Afghanistan’ শব্দটিতে ১১ অক্ষর রয়েছে; ইংরেজি ‘The Pentagon’ শব্দটিতে ১১ অক্ষর রয়েছে ইত্যাদি ইত্যাদি। Ernest Vincent Wright (১৮৭৩-১৯৩৯) নামের একজন মার্কিন লেখক Gadsby: Champion of Youth (Wetzel Publishing Co, ১৯৩৯) নামে পঞ্চাশ হাজার একশ দশ শব্দের এক উপন্যাস লিখেছিলেন। যেখানে তিনি ইংরেজি বর্ণ E আছে এমন একটি শব্দও ব্যবহার করেন নি। কোনো ধরনের ব্যাকরণগত ভুল, বাক্যের অসামঞ্জস্যতা, ভাব প্রকাশের দুর্বলতাবিহীন এ উপন্যাসে ব্যবহৃত হয়নি he, she, they, them, theirs, her, herself, myself, himself, yourself, love, hate-এর মতো শব্দ[২৪৩]!
আসলে একটু মাথা খাটালে পৃথিবীর প্রায় সকল বিষয় নিয়েই সংখ্যাতত্বের খেলা সম্ভব। সেটি গণিতবিদদের দ্বারা সমর্থিত না হলেও মানুষকে আনন্দ কিংবা ধাঁধায় ফেলার জন্য যথেষ্ট।
ধরুন, একটি সমুদ্র সৈকত। আপনি একটি নিক্তি নিলেন এবং সমুদ্র সৈকতের একটি একটি করে বালুর ওজন মাপা শুরু করলেন। যেসব বালুর ওজন হচ্ছে এক গ্রাম সেটিকে আপনি থলেতে ভরে রাখলেন। যেগুলো না সেগুলো ফেলে দিলেন। আরও ধরি, আপনার হাতে অফুরন্ত সময় রয়েছে এবং এই অফুরন্ত সময় আপনি শুধু বালুর ওজন মাপবেন এবং এক গ্রামের ওজনের বালু আলাদা করবেন। তাহলে দীর্ঘসময় পর আপনি বেশ বড় একটি বালুর স্যাম্পল জোগাড় করতে পারবেন। যাদের প্রত্যেকের ওজন এক গ্রাম করে। এখন যদি আপনি ঘোষণা দেন যে, এই সমুদ্র সৈকতটি একটি মিরাকল এবং এর প্রত্যেকটি বালু কণার ওজন এক গ্রাম তাহলে কী তা যুক্তিসংগত হবে? হবে না। কারণ গণিত আমাদের বলে, এই সৈকতে প্রতিটি বালুকণার ওজন এক গ্রাম-এই শর্ত আরোপ করার আগে আপনাকে শতকরা কতভাগ বালুর ওজন এক গ্রাম তা নির্ণয় করতে হবে। যদি শতকরা মান ৯০-৯৯% হয় তাহলে আমরা সেই শর্ত সঠিক বলে ধরে নিতে পারি।
শতকরা= [এক গ্রাম ওজন এমন বালুর সংখ্যা/পরীক্ষণীয় মোট বালুর সংখ্যা (যে বালু আপনি ফেলে দিয়েছেন। যে বালু আপনি রেখেছেন) ] x ১০০
আপনার পরীক্ষায় এক বস্তা বালুর বিপরীতে কমপক্ষে এক হাজার বস্তা বালু আপনি বাদ দিয়েছেন (কারণ তাদের ওজন এক গ্রাম নয়)। সুতরাং আপনার শতকরা মান হবে খুব কম। অর্থাৎ মিরাকলটি সত্যি নয়। মূল ব্যাপার হলো, যেকোনো বই থেকেই আপনি ‘বিশেষ কিছু অংশ/অপশন বাছাই করতে পারেন। তারপর যেই যেই অপশন আপনার মিরাকল প্রমাণে কাজে লাগবে তা রেখে (ধরুন সাত দ্বারা বিভাজ্য) বাকিগুলো ফেলে দিতে পারেন। কোরআনের ক্ষেত্রে যেমন, একটি শব্দের অষ্কর সংখ্যা, চ্যাপ্টারের সংখ্যা, নির্দিষ্ট একটি শব্দ সর্বমোট কতবার ব্যবহৃত হয়েছে সেই সংখ্যা ইত্যাদি-ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়েছে। ঠিক তেমনিভাবে আপনি চাইলে অন্য একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা, বিজোড় সুরার সংখ্যা, জোড় চ্যাপ্টারের সংখ্যা, বিজোড় চ্যাপ্টারে কতটি অক্ষর রয়েছে-জোড়টিতে কতটি রয়েছে ইত্যাদি নিতে পারেন। অর্থাৎ আপনি মাথা খাটিয়ে অসীমসংখ্যক অপশন/বিশেষ অংশ বাছাই করতে পারেন। ডক্টর খালিফা তাই করেছেন। অসংখ্য অপশন থেকে তিনি উনিশ দ্বারা বিভাজ্য প্রমাণ করা যায় এমন অপশনগুলো গ্রহণ করেছেন-বাকিগুলো ফেলে দিয়েছেন। কিন্তু কোরআনে যদি আসলেই উনিশের মিরাকল থেকে থাকে তাহলে তা সবকিছুতেই থাকবে-শুধু কয়েকটি জিনিসে নয়। যেমন, কোরআনের রুকু সংখ্যা ৫৪০টি, ৩০টি পারা, ৭টি মঞ্জিল রয়েছে, যেগুলো ১৯ দিয়ে নিঃশেষে বিভাজ্য হতে পারত। ২৩ বছর ধরে কোরআন নাজিল হয়েছে সুতরাং ২৩ সংখ্যাটি ১৯ দ্বারা বিভাজ্য হতে পারত, মুহাম্মদ ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত লাভ করেন, সেটি ১৯ দ্বারা বিভাজ্য হতে পারত, কোরআনের প্রতিটি আয়াতের শব্দ ও বর্ণ সংখ্যা ১৯ দিয়ে বিভাজ্য হতে পারত। কিন্তু হয় নি[২৪৪]।
জল অনেক ঘোলা ইতোমধ্যেই হয়ে গেল। পাঠক হয়ত এখন মনে মনে ভাবছেন, তাতে কী হয়েছে, কতগুলোতেই তো গাণিতিক মিল রয়েছে, ব্যাপারটি অলৌকিক হওয়াই স্বাভাবিক। তবে জেনে রাখুন, লৌকিক বিষয়কে অলৌকিকে রূপান্তরিত করে দর্শকদের মোহাচ্ছন্ন করার জন্য আসলে আশ্রয় নিতে হয় মিথ্যা, প্রতারণার। খলিফাও সেই সূত্র লঙ্ঘন করেন নি। একটি বিষয় নিয়েই আলোচনা করা যাক।
ডক্টর রাশাদ খলিফা বলেন—
The key to Muhammad’s perpetual miracle is found in the very first verse of the Qur’an, ‘IN THE NAME OF GOD, MOST GRACIOUS, MOST MERCIFUL = BISM ALLaH, AL RaHMAN, AL-RAHIM…
মুহাম্মদের বলে যাওয়া-কোরআন যে একটি মিরাকল তার সন্ধান লাভ করা যায়, কোরআনের সর্ব প্রথম আয়াতেই–
IN THE NAME OF GOD, MOST GRACIOUS, MOST MERCIFUL = BISM ALLaH, AL-RaHMAN, AL-RAHIM…
এই প্রথম আয়াতের অক্ষর গণনা করে (ইংরেজিতে শুধু বড় হাতের অক্ষর) আমরা দেখতে পাই যে, এখানে উনিশটি অক্ষর রয়েছে। এবং এতে যে শব্দগুলো রয়েছে সেগুলো প্রত্যেকটি উনিশের গুণিতক। যেমন প্রথম অক্ষর, ISM উনিশ বার; দ্বিতীয় শব্দ, ALLaH ২৬৯৮ বার, যা ১৯-এর গুণিতক (১৯ বার ১৪২); তৃতীয় শব্দ, AL-RaHMaN আছে ৫৭ বার, (১৯ বার ৩); সর্বশেষ শব্দ, AL RaHIM আছে ১১৪ বার (১৯ বার ৬)।
ড. খালিফা দাবি করেছেন, কোরআনের এই অলৌকিকত্বে মানুষের কোনো হাত নেই। অথচ, ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ বাক্যে যে ১৯টি বর্ণ আছে, এই মৌলিক দাবিতেই মানুষের হাত আছে। আরবি বাক্যটিকে ইংরেজিতে প্রতিবর্ণীকরণ করার সময় আমরা যদি স্বরবর্ণ বাদ দেই, তাহলে বাক্যটি এরকম দাঁড়ায় : BSM ALLH ALRHMN ALRHIM, উল্লেখ্য, আরবিতে স্বরবর্ণগুলো লেখা হয় না, পড়ার সময় ধরে নেওয়া হয়। এই প্রতিবর্ণীকৃত বাক্যে বর্ণের সংখ্যা ১৯। কিন্তু, আরবিতে ‘তাশদিদ’ বলে একটি প্রতীক আছে, কোনো বর্ণের ওপর সে প্রতীক থাকলে তা দুই বার উচ্চারণ করতে হয়। ALLAH শব্দের দ্বিতীয় L-এর ওপর একটি তাশদিদ আছে। সেক্ষেত্রে এই লাম দুই বার উচ্চারণ করে এভাবে লেখা যেত (বা এভাবে লেখা উচিত) : ALLLAH; আর বর্ণ সংখ্যা হয়ে যেত ২০টি।
তাশদিদ যুক্ত বর্ণ দুই বার ধরা হয়েছে নাকি এক বার ধরা হয়েছে, সে বিষয়টি ড. খালিফা কোথাও স্পষ্ট করে বলেন নি। এছাড়া যে স্বরবর্ণগুলো লেখা হয় না, কিন্তু পড়ার সময় ধরা হয় সেগুলো অন্তর্ভুক্ত করা বা। বাদ দেওয়ার ব্যাপারটাও তিনি স্পষ্ট করেন নি।
পরবর্তী সমস্যা BISM শব্দ নিয়ে। এটি প্রকৃতপক্ষে দুটি শব্দের সমন্বয় : Bi (এক্ষেত্রে এই শব্দের অর্থ ‘মধ্যে) এবং ISM (অর্থ ‘নাম)।
ড. খালিফা সবসময় আরবি বর্ণক্রম ব্যবহারের কথা বলেছেন। এই আরবি বর্ণক্রম ব্যবহার করে ISM শব্দটির অনুসন্ধান করা যেতে পারে। আবদুল বাকি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কোরআনের একটি নির্ঘণ্ট ঘেঁটে এই আশ্চর্যজনক তথ্য পাওয়া গেছে।
BiSM শব্দটি কোরআনের প্রথম আয়াতেই আছে। এই শব্দটি কোরআনের মাত্র তিনটি স্থানে উল্লেখিত হয়েছে : ১ : ১১, ১১ : ৪১ এবং ২৭ : ৩০] কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে কেবল ISM শব্দটি কোরআনে মোট ১৯ বার উল্লেখিত হয়েছে।
কিন্তু তৃতীয় আরেকটি তালিকা আছে। ISMuHu শব্দের অর্থ ‘তার নাম। এটি আরবিতে একটি অখণ্ড শব্দ হিসেবে লেখা হয়। কোরআনে এটি ৫ বার এসেছে।
সবগুলো ফল যোগ করলে পাওয়া যায় : ৩ + ১৯ + ৫ = ২৭, স্পষ্টতই এখানে ১৯ এর সাংখ্যিক তাৎপর্য আর থাকছে না।
আমাদের সামনে আরও অনেকগুলো অনুমানের ব্যাপার আছে, যেগুলো সম্বন্ধে ড. খালিফা কোনো ব্যাখ্যা দেন নি। কোন বিবেচনায় তিনি তিনবার উল্লেখিত BiSM শব্দটি গণনা থেকে বাদ দিয়েছেন? যে শব্দ নিয়ে গবেষণা করছিলেন সেই শব্দটিই বাদ দেওয়ার পিছনে কোনো যুক্তিই দেখান নি। আর কেবল বিচ্ছিন্ন ISM শব্দ গণনার ব্যাপারেই বা তিনি কোন নীতি অনুসরণ করেছেন? সর্বনামযুক্ত বিশেষ্য ISMuHu-কে কেন বাদ দিলেন?
তাহলে কি এই তিন ধরনের শব্দের অর্থের মধ্যে কোনো ব্যাখ্যা লুকিয়ে আছে? হয়তবা, যেসব স্থানে এই শব্দগুলোর মাধ্যমে কেবল আল্লাহর নাম বোঝানো হয়েছে সেগুলোকেই ড. খালিফা গণনা করেছেন। কিন্তু নিম্নোক্ত দুটি আয়াতের দিকে লক্ষ্য করলে এই ধারণাও ভুল বলে প্রমাণিত হয়। সুরা মায়িদার ৫ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–
…but pronounce God’s name (ISM ALLaH) over it…
এবং সুরা বাকারার ১১৪ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে–
And who is more unjust than he who forbids in places for the worship of God, that His name (ISMuHu) should be pronounced?
মূল আরবি বা ইংরেজি অনুবাদ কোনোটিতেই এই শব্দগুলোর মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই, একটি ছাড়া : এখানে ‘God’s name সরাসরি বিধেয় এবং His name উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবি বর্ণক্রমে এই শব্দ দুটির লেখ্য রূপের ভিত্তিতেই কেবল দুটিকে ভিন্নস্থানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।
আরও কথা আছে, কিসের ভিত্তিতেই বা ড. খালিফা এই শব্দগুলোর বহুবচন রূপগুলো বাদ দিলেন? এগুলোর বহুবচন কোরআনে আরও ১২ বার এসেছে। বিশেষত সুরা আ’রাফের ১৪০ নম্বর আয়াতের কথা উল্লেখ করা MT, ‘The most beautiful names belong to God…’
বহুবচন বাদ দেওয়ার কেবল একটি কারণই থাকতে পারে। সেটি হচ্ছে, বহুবচনগুলো গণনা করলে মোট সংখ্যাটি ১৯ না হয়ে ৩৯ হয়ে যায়।
উপর ALLAH শব্দটির ব্যবহারের ধরনের ব্যাপারেও সন্দেহ আছে। এই শব্দের সাথে যখন Li উপসর্গ যুক্ত হয় তখন দুইয়ে মিলে LiLaH বা LiLLah শব্দের জন্ম দেয়। এখানে উপসর্গটির অর্থ প্রতি। এই লিল্লাহ শব্দেও একটি লাম-এর উপর তাশদিদ আছে। (উদাহরণ হিসেবে ২ : ২২ আয়াতটি দেখা যেতে পারে) ব্যাকরণ অনুসারে এই প্র উপসর্গযুক্ত শব্দটি ঠিক BiSM-এর মতো করেই ব্যবহৃত হয়। পূর্বের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি ড. খালিফা এবার প্র উপসর্গযুক্ত শব্দগুলো বাদ দিয়ে কেবল মূল শব্দটিই গণনা করবেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। এবার ঠিকই LiLaH গুলো গণনা করেছেন, কারণ এগুলো গণনা না করলে মোট সংখ্যাটা ২৬৯৮ হতো না এবং তা ১৯ দিয়েও বিভাজ্য হতো না। এধরনের যাদৃচ্ছিক ব্যবহারের পেছনে কি আদৌ কোনো যুক্তি আছে?
ISM এর সাথে Bi যুক্ত হয়ে যখন BiSM হয়েছে তখন ড. খালিফা সেটা বাদ দিয়েছেন, কিন্তু ALLAH-র সাথে Li যুক্ত হয়ে যখন LiLaH হয়েছে তখন তিনি সেগুলো ঠিকই গণনা করেছেন; এ কেবল ১৯ দিয়ে বিভাজ্য একটি সংখ্যায় পৌঁছানোর জন্য।
AL-RaHMaN শব্দের ক্ষেত্রে কোনো দ্বিধা নেই। এটি কোরআনে ৫৭ (১৯ বার ৩) বারই উল্লেখিত হয়েছে। লেখকও এমনটিই বলেছেন।
এবার AL-RaHIM শব্দের দিকে দৃষ্টি দেওয়া যাক। ড. খালিফা বলেছেন, এই শব্দ মোট ১১৪ (৬ বার ১৯) বার এসেছে। কিন্তু আবদুল-বাকির নির্ঘণ্ট অনুসারে কোরআনে এই শব্দটি হুবহু এই রূপে মাত্র ৩৪ বার উল্লেখিত হয়েছে। অর্থাৎ এই ৩৪ স্থানেই শব্দের আগে AL নামক ডেফিনিট আর্টিক্যালটি আছে। কিন্তু বাকি ৮১ স্থানে শব্দের আগে কোনো ডেফিনিট আর্টিক্যাল নেই। এখন আর্টিক্যালসহ এবং ছাড়া সবগুলোই যদি আমরা গণনা করি, তাহলে মোট সংখ্যাটি দাঁড়ায় ১১৫] এক বার এর বহুবচনও উল্লেখিত হয়েছে। তাহলে মোট ১১৬ হয়ে যাচ্ছে১১৫ এবং ১১৬, কোনোটিই ১৯ দ্বারা বিভাজ্য নয়।
ড. খালিফার এই আবিষ্কারকে অনেকেই সম্পূর্ণ অনুমোদন দিয়েছেন। ড. Bechir Torki এ নিয়ে রীতিমতো ৪ পৃষ্ঠার এক বিশাল সারাংশ রচনা করেছেন। এইসবগুলো অনুমোদনপত্র বা সারাংশতেও উপরে উল্লেখিত চারটি মৌলিক অনুমিতির ব্যাপার সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।
ড. খালিফা ALLAH শব্দে তাশদিদের কারণে দ্বিত্ব হয়ে যাওয়া লামগুলো গণনা থেকে বাদ দিয়েছেন, আবার অলিখিত স্বরবর্ণগুলোও বাদ দিয়েছেন।
তিনি ISM এর মোট সংখ্যা গণনা করতে গিযে BiSM শব্দটি সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন, কিন্তু ওদিকে আবার ALLaH শব্দ গণনা করতে গিযে LiLaH অন্তর্ভুক্ত করেছেন।
এছাড়াও তিনি তার গণনা থেকে ISMuHu বাদ দিয়েছেন, যদিও ব্যাকরণগত দিক দিয়ে এটি হুবহু ISM এর মতোই অর্থ বহন করে।
এছাড়া তিনি ISM এবং AL-RaHIM শব্দের বহুবচন রূপগুলো বাদ দিয়েছেন। উপরন্তু তার AL-RaHIM শব্দের গণনা ভুল হয়েছে।
সুতরাং মিরাকল প্রমাণের জন্য খলিফা নিজের ইচ্ছামতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন-’মিলিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু সে ব্যাপারে কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করেন নি। তার অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলোও একই দোষে দোষী। সেগুলো এবং অন্যান্য বিভিন্ন ঘটনার গাণিতিক মিরাকল নিয়ে বাংলা ব্লগের অন্যতম লেখা হিসেবে প্রকাশিত মুক্তমনায় সৈকত চৌধুরী এবং অনন্ত বিজয় দাশের লেখা, কোরআনের ‘মিরাকল ১৯’-এর উনিশ-বিশ245! তাদের এ প্রবন্ধটি শুদ্ধস্বর থেকে প্রকাশিত ‘পার্থিব (২০১১) বইয়েও সঙ্কলিত হয়েছে।
.
সবই ব্যাদে আছে
এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ওই অনলাইন পত্রিকাটিতে অধ্যাপক ভদ্রলোকের সাথে বিতর্কের কারণে কোরআন এবং কোরআন-বিশেষজ্ঞদের কথা বারে বারে উঠে এসেছে বলে এমন ভাবার কোনো কারণ নেই যে অন্যান্য ধর্মের ‘কিতাব বিশেষজ্ঞের দল’ এই অভিযোগ থেকে মুক্ত। এরা কেউই আসলে ধোয়া তুলসিপাতা নয়; বরং, একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। কিছু হিন্দু ভাববাদী ‘বৈজ্ঞানিক আছেন, যারা মনে করেন মহাভারতে কৃষ্ণ অর্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছে তা আসলে বিগব্যাং ছাড়া কিছু নয়। মৃণাল দাসগুপ্ত ভারতের জাতীয় বিজ্ঞান আকাঁদেমির বিখ্যাত বিজ্ঞানী। উনি দাবি করেন, আজ আধুনিক বিজ্ঞান যে সমস্ত নতুন তত্ত্ব ও তথ্য প্রতিদিনই আবিষ্কার করছে, তার সবকিছুই নাকি প্রাচীনকালের মুনি ঋষিরা বের করে গেছেন। বেদে নাকি সেসমস্ত আবিষ্কার ‘খুবই পরিষ্কারভাবে লিপিবদ্ধ আছে। মি. দাসগুপ্তের ভাষায়, রবার্ট ওপেনহেইমারের মতো বিজ্ঞানীও নাকি গীতার বিশ্বরূপ দর্শনে এতই অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন যে ল্যাবরেটরিতে আণবিক শক্তির তেজ দেখে নাকি গীতা থেকে আবৃত্তি করেছিলেন–
দিবি সূৰ্য্যসহস্রস্য ভবেদ যুগপদুথিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা সাদ ভাসন্তস মহাত্মনঃ
বিজ্ঞান জানা কিছু শিক্ষিত হিন্দু বুদ্ধিজীবী আছেন যারা ভাবেন আধুনিক বিজ্ঞান আজ যা আবিষ্কার করছে, তা সবই হিন্দু পুরাণগুলোতে লিপিবদ্ধ জ্ঞানের পুনরাবৃত্তি। হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান রামকৃষ্ণ মিশন তাদের মুখপত্র ‘উদ্বোধন’-এ বলা শুরু করেছে যে, কৃষ্ণগহ্বর কিংবা সময় ধারণা নাকি মোটেই নতুন কিছু নয়। হিন্দুধর্ম নাকি অনেক আগেই এগুলো জানতে পেরেছিল। কীভাবে? ওই যে বহুল প্রচারিত সেই আপ্তবাক্যে ‘ব্রহ্মার এক মুহূর্ত পৃথিবীর সহস্র বছরের সমান’L কিছু ধর্মবাদীর দৃষ্টিতে মহাভারতের কাল্পনিক কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ছিল আসলে এক ‘পারমাণবিক যুদ্ধ’ (Atomic War)। প্রশান্ত প্রামাণিক নামে ভারতের এক জনপ্রিয় বিজ্ঞান লেখক’ ‘ভারতীয় দর্শনে আধুনিক বিজ্ঞান বইয়ে তার কল্পনার ফানুসকে মহেঞ্জোদারো পর্যন্ত টেনে নিয়ে বলেছেন-’সম্ভবত দুর্যোধনেরই কোনো মিত্র শক্তি পারমাণবিক যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে থাকবে মহেঞ্জোদারোতে’ (পৃ. ৬)। ‘সবই ব্যাদে আছে’ মার্কা এইসব বকচ্ছপ ভাববাদীরা অবলীলায় দাবি করে ফেলেন যে, নলজাতক শিশু (Test Tube Baby) আর বিকল্প মা (Surrogate Mother) আধুনিক বিজ্ঞানের দান মনে করা হলেও তা হিন্দু সভ্যতার কাছে নাকি নতুন কিছু নয়। দ্রোণ-দ্রোণী, কৃপ-কৃপীর জন্মের পৌরাণিক কাহিনিগুলো তারই প্রমাণ। এমনকি কিছুদিন আগে উপসাগরীয় যুদ্ধে ব্যবহৃত স্কাড আর প্যাট্রিয়ট মিসাইল নাকি হিন্দু পুরাণে বর্ণিত ‘বরুণ বাণ’ আর ‘অগ্নিবাণ’ বই কিছু নয়। তারা সবকিছুতেই এমনতর মিল পেয়ে যান। যেমনিভাবে ভারতের ‘দেশ’-এর মতো প্রগতিশীল পত্রিকায় ২২ এপ্রিল ১৯৯৫ সংখ্যায় প্রকাশিত বিজ্ঞান ও ভগবান’ নিবন্ধের লেখক হৃষীকেশ সেন বেদান্তে বর্ণিত উর্ণনাভ বা মাকড়শার মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মডেলের মিল পেয়ে গেছেন।
খ্রিস্টান সমাজেও এই ধরনের ‘হাসজারু’ প্রচেষ্টা বিরল নয়। বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্ক টিপলার পদার্থবিজ্ঞানে অবদানের জন্য ইদানীং যত না বিখ্যাত, তার চেয়ে বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছেন খ্রিস্টধর্মকে ‘বিজ্ঞান’ বানানোর জন্য। ওমেগা পয়েন্ট নামে একটি ধারণা দিয়েছেন টিপলার যা মহাসংকোচন (বিগ ক্রাঞ্চ)–এর সময় সিংগুলারিটির গাণিতিক মডেলকে তুলে ধরে। এ পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু টিপলার মনে করেন এই ওমেগা পয়েন্টই হচ্ছে ‘গড’। শুধু তাই নয়, যিশুর অলৌকিক জন্মকে (ভার্জিন বার্থ) তিনি বৈজ্ঞানিক বৈধতা দিতে চান যিশুকে বিরল xx male বানিয়ে, যিশুর পুনরুত্থানকে ব্যারন অ্যানাইহিলেশন প্রক্রিয়ার সাথে তুলনা করেছেন, ইনকারনেশন বা অবতারকে বলেছেন বিপরীতমুখী ডিম্যাটেরিয়ালাইজেশন পদ্ধতি, ইত্যাদি। এ সমস্ত রঙ-বেরঙের গালগপ্প নিয়েই তার সাম্প্রতিক বই The Physics of Christianity (2007)! বলা বাহুল্য মাইকেল শারমার, ভিক্টর স্টেঙ্গর, লরেন্স। ক্রাউসসহ অনেক বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকই টিপলারের যুক্তিকে খণ্ডন করেছেন[২৪৬], কিন্তু তাতে অবশ্য আধুনিক ‘বিজ্ঞানময় খ্রিস্টধর্মোন্মাদনা থেমে যায় নি, যাবেও না। ফ্রাঙ্ক টিপলারের অনেক আগে ১৯৭৫ সালে ফ্রিজোফ কাপরা একই মানসপটে লিখেছিলেন ‘The Tao of Physics’– প্রাচ্যের তাওইজমের সাথে বিজ্ঞানকে জুড়ে দিয়ে। চীনের প্রাচীন দার্শনিকেরা ইন এবং য্যান (yin and yang) নামে পরস্পরবিরোধী কিন্তু একীভূত সত্ত্বার কথা বলেছিলেন মানুষের মনে ভালো-মন্দ মিলেমিশে থাকার প্রসঙ্গে। ফ্রিজোফ কাপরা সেই ইন এবং ই্যাংকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিলেন কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার জগতে পদার্থের দ্বৈত সত্ত্বার (dual nature of matter) বর্ণনা হাজির করে, পদার্থ যেখানে কখনও কণা হিসেবে বিরাজ করে, কখনোবা তরঙ্গ হিসেবে। আধুনিক পদার্থবিদ্যার শূন্যতার ধারণাকে মিলিয়ে দিয়েছেন তাওইজমের ‘চী’ (chi or qi)-এর সাথে–
যখন কেউ জানবে যে, মহাশূন্য ‘চী’ দিয়ে পরিপূর্ণ, তখনই কেবল সে অনুধাবন করবে, শূন্যতা বলে আসলে কিছু নেই।
মুক্তমনার বিশিষ্ট সদস্য ‘অপার্থিব জামান’ ধর্মগ্রন্থের মধ্যে বিজ্ঞান খোঁজার এই অপচেষ্টার বিরুদ্ধে একটি নিবন্ধে লিখেছিলেন–
প্রায়শই ধর্মবাদীরা ধর্মগ্রন্থের একটি নির্দিষ্ট আয়াত বা শ্লোকের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞান খুঁজে পান। এটি একটি হাস্যকর অপচেষ্টা। ওমনিভাবে খুঁজতে চাইলে যেকোনো কিছুতেই বিজ্ঞানকে খুঁজে নেওয়া সম্ভব। যেকোনো রাম-শ্যাম-যদু-মধু আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ব আবিষ্কারের অনেক আগে কোনো কারণে বলে থাকতে পারে- ‘সবকিছুই আসলে আপেক্ষিক। কিন্তু আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ব আবিষ্কারের পর সেই সমস্ত রাম শ্যাম-যদু-মধুরা যদি দাবি করে বসে এই বলে ‘হুঁ! আমি তো আইনস্টাইনের আগেই জানতাম আপেক্ষিক তত্বের কথা’ তবে তা শুধু হাস্যকরই নয়, যে সমস্ত নিবেদিতপ্রাণ বিজ্ঞানীরা তাদের শ্রমলব্ধ গবেষণার মাধ্যমে নিত্য-নতুন আবিষ্কারে পৃথিবীবাসীকে উপকৃত করে চলেছেন, তাদের প্রতি চরম অবমাননাকরও বটে। সবাই জানে, আপেক্ষিক তত্ব আবিষ্কারের জন্য আইনস্টাইনকে কখনোই কোনো ধর্মগ্রন্থের সাহায্য নিতে হয় নি, বরং আপেক্ষিক তত্ব আবিষ্কারের পর পরই তা ধর্মবাদীরা নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থে জুড়ে দেওয়ার জন্য নানা জায়গায় মিল খুঁজে পেতে শুরু করলেন। বলা বাহুল্য, আধুনিক বিজ্ঞান যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দানে এখনও অক্ষম, সেই সমস্ত জায়গায়। ধর্মবাদীরাও কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে নীরব। যেমন, বিজ্ঞান এখনও নিশ্চিতভাবে জানে না যে আমাদের এই মহাবিশ্ব বদ্ধ, খোলা নাকি ফ্ল্যাট। তাই ধর্মবাদীদেরও কেউ তাদের ঐশী কিতাব থেকে আমাদের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী করে কোনো ধরনের আলোকপাত করতে পারছেন না। কিন্তু আমি নিশ্চিত যে, বিজ্ঞানের কল্যাণে কথনও যদি। এর উত্তর বেরিয়ে আসে, তবে সাথে সাথে ধর্মবাদীরা বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের কতকগুলো অস্পষ্ট আয়াত অথবা শ্লোক হাজির করে এর অতিপ্রাকৃত দাবি করবেন। মূলত প্রতিটি ক্ষেত্রেই (গোঁজা) মিলগুলো পাওয়া যায় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো প্রকাশ পাওয়ার পর, তার আগে নয়। এ কি স্রেফ ঘটনার কাকতালীয় সমাপতন?
আমরা অপার্থিব জামানের মন্তব্যের সাথে সামগ্রিকভাবে একমত। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধর্মগ্রন্থে ‘আধুনিক বিজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া যায়, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলো প্রকাশ পাওয়ার পর, তার আগে নয়। কারণ বিজ্ঞানের দায় পড়ে নি ধর্মগ্রন্থ থেকে দীক্ষা নিয়ে আলোর সন্ধান লাভ করতে, বরং ধর্মগুলোই জেনে গেছে, বিজ্ঞান ছাড়া তারা টিকে থাকতে পারবে না। কাজেই, নিত্যনতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলোকে ধর্মগ্রন্থের সাথে জুড়ে দেওয়ার জন্য ধর্মবাদীরা এখন মুখিয়ে থাকে। একটা সময় বাইবেল-বিরোধী সূর্যকেন্দ্রিক তত্ব প্রকাশের জন্য কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, ব্রুনোর ওপর অত্যাচারের স্টিমরোলার চালিয়েছিল বাইবেল-ওয়ালারা, সেই তারাই এখন বাইবেলের নানা জায়গায় সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্বের ‘আলামত’ পেয়ে যান। কোরআনের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার থাটে। কিছুদিন আগেও দেখতাম অনেকেই ডারউইনের বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধে রীতিমতো জিহাদ শুরু করেছিলেন কোরআনের আয়াতকে উদ্ধৃত করে। আজকে বিবর্তনতত্ত্বের সপক্ষের প্রমাণগুলো এতই জোরালো হয়ে উঠেছে যে, সেগুলোকে আর অস্বীকার করা যাচ্ছে না। তাই শুরু হয়েছে বিবর্তনবাদের সপক্ষে আয়াত খোঁজা। পেয়েও গেছেন কিছু কিছু একটা ওয়েবসাইটে দেখলাম, ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে যে, কোরআনের ৪ : ১, ৭ : ১১, ১৫ : ২৮-২৯, ৭৬ : ১-২ প্রভৃতি আয়াতগুলো নাকি বিবর্তন তত্ত্বের ‘সরাসরি’ প্রমাণ। এ সমস্ত আয়াতে ‘সৃষ্টি’ বোঝাতে ‘খালাকা’ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ‘গ্র্যাজুয়াল চেঞ্জ’ অতএব ইহা বিবর্তন’। অনুমান আর কয়েক বছরের মধ্যে শুধু বিবর্তন নয়, অচিরেই তারা মাল্টিভার্স, কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশন, স্ট্রিং তত্ব, প্যান্সপারমিয়া, জেনেটিক কোড, মিউটেশন এধরনের অনেক কিছুই ধর্মগ্রন্থে পেয়ে যাবেন (কিছু কিছু হয়ত এর মধ্যেই পেয়েও গেছেন)। তবে এধরনের সমন্বয়ের চমৎকার খেলা দেখিয়েছে হিন্দু ধর্মবাদীরাই। যখন বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকে ফ্রেডরিক হয়েল, হারমান বন্দি আর জযন্ত নারলিকার মিলে স্থিতিশীল মহাবিশ্ব তত্ত্বের (Steady state theory) অবতারণা করেছিলেন, তখন তা ভারতের হিন্দুত্ববাদীদের মধ্যে তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। কারণ এটি বেদে বর্ণিত ‘চির শাশ্বত’ মহাবিশ্বের ধারণার সাথে মিলে যায়। কিন্তু মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণের (Cosmic background radiation) খোঁজ যখন বিজ্ঞানীরা পেলেন, তখন তা স্থিতিশীল মহাবিশ্বকে হটিযে মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব বা বিগব্যাংকে বৈজ্ঞানিক সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে দিল। হিন্দুত্ববাদীরাও সাথে সাথে ভোল পালটে ‘চির শাশ্বত’ মহাবিশ্ব বাদ দিয়ে ‘অদ্বৈত ব্রহ্ম’র খোঁজ পেয়ে গেলেন। অর্থাৎ, মহাবিশ্বের সৃষ্টি থাকুক, না থাকুক, চিরশাশ্বত হোক আর না হোক, স্থিতিশীল হোক আর অস্থিতিশীলই হোক সবই কিন্তু তাদের ধর্মগ্রন্থে আছে।
ধর্মবাদীদের গোঁজামিল দেওয়ার এই প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা (সঠিকভাবে বললে ‘অপচেষ্টা’) দেথে প্রবীর ঘোষ তার আমি কেন ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না বইতে খুবই মজার একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন–
ধরা যাক, রাস্তার একটি মাতালকে এই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডের মডেল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। মাতালটি হয়ত রক্ত-চোখে প্রশ্নকারীর দিকে তাকিয়ে থেকে রাস্তা থেকে পড়ে থাকা মদের বোতলটি তুলে নিয়ে ঢক ঢক করে গলায় মদ ঢালতে শুরু করল। তারপর অবশেষে শূন্য বোতলটি রাস্তায় ফেলে দিয়ে হেঁটে চলে গেল। পুরো ব্যাপারটিকে কিন্তু ইচ্ছে করলেই বিশ্ব ব্রান্ডের সাথে গোঁজামিল দিয়ে জুড়ে দেওয়া যায়। মদের বোতলটি যখন পূর্ণ ছিল, সেই অবস্থাটিকে আমাদের এখনকার প্রসারণশীল মহাবিশ্বের সাথে তুলনা করা যায়। মাতালটি গলায় মদ ঢেলে বোতল খালি করতে শুরু করল এই বোঝাতে যে, এক সময় বিশ্বের এই প্রসারণ থেমে যাবে আর শুরু হবে সংকোচন। শেষ পর্যন্ত মাতালটি শূন্য বোতল রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এটাই বোঝাতে চাইছে যে মহাবিশ্ব সংকুচিত হতে হতে পূর্বের সমস্ত সৃষ্টিকে ধ্বংস করে সিংগুলারিটি বিন্দুতে চলে আসবে।
কী অদ্ভুত ‘মহা-বিজ্ঞানময়’ নির্বুদ্ধিতা! বাংলাদেশে বেশ ক’বছর ধরেই চলছে এই নির্বুদ্ধিতার খেলা, মাতাল সাজার আর মাতাল বানানোর নিরন্তর প্রক্রিয়া। এখানে ‘জ্ঞানের কথা’, ‘লজ্জা’ ‘নারী’র মতো প্রগতিশীল বই অবলীলায় নিষিদ্ধ করা হয় মানুষের ‘ধর্মানুভূতি’-তে আঘাত লাগার অজুহাতে, আরজ আলী মাতুব্বরের ‘সত্যের সন্ধান’ আর দেবীপ্রসাদ চৌধুরীর ‘যে গল্পের শেষ নেই’ পড়ার অপরাধে মুক্তিযোদ্ধা ওহাবকে ‘জুতোর মালা পরিয়ে সারা গ্রাম ঘোরানো হয়, তসলিমাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা হয়, মুক্তবুদ্ধির চর্চা করার জন্য আহমেদ শরীফ-আলী আসগর-কবীর চৌধুরীদের ‘মুরতাদ’ ঘোষণা করা হয়, চাপাতির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হতে হয় মুক্তমনা অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদকে, আর অপরপক্ষে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে বের করা হয় ‘Scientific Identification in Holy Quran2-93 মতো ছদ্ম-বিজ্ঞানময় গ্রন্থ। ভক্তি-রসের বান ডেকে অদৃষ্টবাদ আর অলৌকিকত্বের রমরমা বাজার তৈরি করতে চলছে বুকাইলি-মুর-দানিকেন-নাযেকদের বইয়ের ব্যাপক প্রচার আর প্রসার। বাংলাদেশের সারা বাজার এখন ‘আল-কোরআন এক মহা বিজ্ঞান, ‘মহাকাশ ও কোরআনের চ্যালেঞ্জ’, ‘বিজ্ঞান না কোরআন’, ‘বিজ্ঞান ও আল কোরআন’ জাতীয় ছদ্ম বৈজ্ঞানিক বইয়ে সয়লাব। মুক্তমনা এবং শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চের যৌথ প্রয়াসে প্রকাশিত ‘স্বতন্ত্র ভাবনা’ (চারদিক, ২০০৮) বইটির ভূমিকায় উদ্ধৃত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অজ্য রাযের একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি–
জ্ঞানের একমাত্র উৎস যদি পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলো হয়, তাহলে সেই সমাজে নেমে আসবে বন্ধ্যাত্ব, সমাজ হবে জড় চেতনা-চিন্তায় আচ্ছন্ন, সৃষ্টিশীলতার স্থান দখল করবে কুসংস্কার, মূর্খতা, কূপমণ্ডুকতা আর অজ্ঞানতা। আমাদের সমাজে দেখা যাচ্ছে কুসংস্কার আর প্রযুক্তিবিদ্যার ফসলকে আত্মস্থ করার পারস্পরিক সহাবস্থান। বিজ্ঞানের যুক্তি চাই না, চাই তার ফসল, পাশে থাক অন্ধবিশ্বাস আর ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ। এই সমাজেই সম্ভব ড্রয়িং রুমে রঙিন টেলিভিশন সেট স্থাপন, এবং হিস্টিরিয়া-আক্রান্ত কন্যাকে পীরের চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রেরণ। এই সমাজেই সম্ভব অণুরসায়নবিদদের রসায়ন চর্চার পাশাপাশি তথাকথিত পীরের পদচুম্বন।
সত্যিই তাই। অদ্ভুত উটের পিঠে সত্যিই বুঝি চলেছে স্বদেশ। বিজ্ঞানের এই অগ্রগামীতার যুগে প্রাত্যহিক জীবনে ধর্মের বাঁধন ক্রমশ যখন শিথিল হয়ে পড়ছে, মানুষের মনে দেখা দিচ্ছে নানা ধরনের সংশয় আর প্রশ্ন তখনই ধর্মকেন্দ্রিক নিবর্তন মূলক শোষণ ব্যবস্থা বজায় রাখার মতলবে শুরু হয়েছে এক নতুন ধরনের নিরন্তর মগজ ধোলাই আর তা হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞানের মোড়কে ধর্মকে পরিবেশন। কিছু মানুষ রসাল চাটনির মতো তা খাচ্ছেও বেশ। ধর্মের নেশায় পুঁদ হয়ে মানুষ ভাবতে শিখছে ১৪০০ বছর আগে লেখা ‘বিজ্ঞানময়’ কিতাবে সত্যিই বুঝি মহা বিস্ফোরণের কথা আছে, অথবা প্রাচীন কোনো শ্লোকে আছে কাল প্রসারণের ইঙ্গিত। কে দেবে এই মোহান্ধ জাতিকে মুক্তি? ওমর খৈয়ামের একটি কবিতার কথা খুব মনে পড়ছে–
যদি মাতালের শিক্ষাকেন্দ্র মাদ্রাসাগুলো
এপিকিউরাস, প্লেটো, অ্যারিস্টটলের দর্শন-শিক্ষালয় হতো,
যদি পীর দরবেশের আস্তানা ও মাজারগুলো
গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতো,
যদি মানুষ ধর্মান্ধতার পরিবর্তে
নীতিজ্ঞানের চর্চা করত,
যদি উপাসনালয়গুলো সর্ববিদ্যাচর্চা-কেন্দ্র
হিসেবে গড়ে উঠত,
ধর্মতত্বের চর্চার পরিবর্তে যদি গণিত বীজ গণিতের।
উন্নতি সাধন করত,
ধর্ম যা মানবজাতিকে বিভক্ত করে তা
‘মানবতা’র দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতো,
পৃথিবী তাহলে বেহেস্তে পরিণত হতো,
পরপারের বেহেস্ত বিদায় নিত,
প্রেম-প্রীতি মুক্তি-আনন্দে জগৎ পরিপূর্ণ হতো নিঃসন্দেহে।
ওমর খৈয়াম বহু বছর আগে যে কথা বলেছিলেন, বাংলাদেশের জন্য সেকথাগুলো আজও কী নিদারুণ সত্য! স্বতন্ত্র ভাবনায় ড. অজয় রায় যেভাবে লিখেছিলেন[২৪৭], তার সাথে সুর মিলিয়ে আমাদেরও বলতে ইচ্ছে করে, ওমর তুমি আর একবার আসো এই দেশে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এই দেশে, ফতোয়াবাজদের এই দেশে আজ তোমার বড় প্রয়োজন।
০৭. ধর্মীয় নৈতিকতা
মানবজাতির অন্য যেকোনো গোত্রের লোকের চেয়ে ধর্মের প্রবর্তক ও প্রচারকেরাই ছিলেন ইতিহাসে যাবতীয় দুর্গতি ও যুদ্ধবিগ্রহের প্রকৃত কারণ। — এডগার অ্যালান পো
ছোটবেলায় এক ভদ্রলোকের বাসায় যেতাম। জ্ঞানী-গুণী কিন্তু রসিক মানুষ। পেশায় অধ্যাপক। আমাদের সাথে শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম আর বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খুব আগ্রহ ভরে আলোচনা করতেন। তার বাড়ির নাম ছিল-সংশয। একদিন না পেরে জিজ্ঞাসাই করে ফেললাম-”সংশ্য কেন? উনি উত্তরে হেসে বললেন ‘সংশ্যই হচ্ছে সকল জ্ঞানের উৎস। মানুষ চোখ-কান বন্ধ করে যে যা বলেছে তা বিশ্বাস না করে সংশয় প্রকাশ করেছে বলেই আমাদের সভ্যতা আজ এতদূর এগিয়েছে। সত্যিই তাই। ইতিহাসের দিকে তাকানো যাক। টলেমির ‘পৃথিবী-কেন্দ্রিক মতবাদে কোপার্নিকাস আর গ্যালিলিওরা সংশয় প্রকাশ করতে পেরেছেন বলেই টলেমির মতবাদ একসময় ভুল প্রমাণিত হয়েছে। পদার্থবিজ্ঞানীরা একসময় ইথার’ নামক কাল্পনিক মাধ্যমটির অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন বলেই পরবর্তীকালে হাইজেনের তরঙ্গ-তত্ব আর ম্যাক্সওযেলের তড়িৎ-চুম্বকীয় তত্ত্বকে সরিয়ে আলোর প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে পদার্থ বিজ্ঞানে জায়গা করে নিয়েছে প্ল্যাঙ্ক, আইনস্টাইন আর ব্ৰগলির তত্ত্বগুলো। হাটন আর লাযেলরা ৬০০০ বছরের পুরনো পৃথিবীর বয়সের বাইবেলের বক্তব্যে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন বলেই মিথ্যা বিশ্বাসকে সরাতে পেরেছিলেন মানুষের মন থেকে। এভাবেই সভ্যতা এগোয়। অনেকেই তর্ক করতে এসে নিজের বিশ্বাসের পক্ষে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেন না; তখন খুব ভক্তি গদ গদ চিত্তে নিরক্ত-বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর’ অথবা মানলে তাল গাছ আর না মানলে গাব গাছ’ ধরনের বাক্যাবলী ব্যবহার করেন। এ যেন ডুবন্ত মানুষের শেষ খড়কুটা আঁকড়ে ধরে অনেকটা যুক্তিহীনভাবেই অন্ধবিশ্বাসের পক্ষে সাফাই গাওয়ার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা। কিন্তু যারা এধরনের বক্তব্য হাজির করেন তারা বোঝেন না যে, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু এধরনের ভাবনা নিয়ে বসে থাকলে আজও বোধকরি সূর্য পৃথিবীর চারিদিকেই ঘুরত। সভ্যতার অনিবার্য গতি আসলে বিশ্বাসের বিপরীতে, যুক্তির অভিমুখে। ক্যারেন আর্মস্ট্রং তার ‘The Battle for God’ বইয়ে যেটিকে একটু গুরুগম্ভীর ভাষায় বলেছেন-”মিথোস থেকে লোগোস-এর দিকে[২৪৪]। এ প্রসঙ্গে গৌতম বুদ্ধেরও একটি চমৎকার উক্তি রয়েছে-Doubt everything, and find your own light. গৌতম বুদ্ধের উক্তিটি যেন আধুনিক যুক্তিবাদীদের সংশযী দৃষ্টিভঙ্গিরই এক সংগঠিত রূপ-যেটি আসলে বলছে, কোনোকিছুই বিনা প্রশ্নে মেনে নিও না! সেই একই সংশয়বাদী ভাবনার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই আধুনিককালে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায়–
বরং দ্বিমত হও, আস্থা রাখো দ্বিতীয় বিদ্যায়।
বরং বিক্ষত হও প্রশ্নের পাথরে।
বরং বুদ্ধির নখে শান দাও, প্রতিবাদ করো।
অন্তত আর যাই করো, সমস্ত কথায়
অনায়াসে সম্মতি দিও না।
কেননা, সমস্ত কথা যারা অনায়াসে মেনে নেয়,
তারা আর কিছুই করে না,
তারা আত্মবিনাশের পথ
পরিষ্কার করে।
সংশয়বাদ নিয়ে সামান্য কটি কথা খুব হালকাভাবে হলেও প্রথমেই সেরে নেওয়া হলো এ কারণে যে, আজ আমরা সংশয়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করব, ব্যবচ্ছেদ করে দেখব আমাদের সমাজের একটি বহুল প্রচলিত মিথকে, যেটি ছোটবেলা থেকেই আমাদের শিখিয়েছে, ধর্ম পালন করা ছাড়া কখনোই ভালোমানুষ হওয়া সম্ভব নয়, সম্ভব নয় সচ্চরিত্রের অধিকারী হওয়া।
.
ধর্ম ও নৈতিকতার খিচুড়ি বনাম রূঢ় বাস্তবতা
প্রাচীনকাল থেকেই ঈশ্বরের প্রতি অগাধ আনুগত্য এবং ধর্ম বিশ্বাসকেই মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের একমাত্র অবলম্বন বলে মনে করা হয়েছে। পাশ্চাত্য বিশ্বে গোঁড়া খ্রিস্টধর্মের অনুসারীরা সংগঠিত হয়ে অনেক আগে থেকেই মগজ ধোলাই করতে শুরু করেছে এ কথা প্রচার করে যে, ধর্মগ্রন্থগুলো আর তাদের ঈশ্বরই একমাত্র নৈতিকতা বিষয়ে শেষ কথা বলার অধিকার রাখে। ধর্মগ্রন্থগুলোতে যেভাবে পথ দেখানো হয়েছে, সেগুলো অন্ধভাবে অনুসরণ করাই হলো নৈতিকতা[২৪৯]। আমাদের দেশি সংস্কৃতি তো আবার এগুলোতে সবসময়ই আবার আরও একধাপ এগিয়ে। অনেক বাসায় দেখেছি সেই ছেলেবেলা থেকেই ছোট ছেলেমেয়েগুলোর মাথা বিগড়ে দিয়ে বাংলা শেখার আগেই বাসায় হুজুর রেখে আরবি পড়ানোর বন্দোবস্ত করানো হয়, নয়ত হরি-কীর্তন শেখানো হয় আর নৈতিক চরিত্র গঠনের মূলমন্ত্র হিসেবে তোতা পাখির মতো আওরানো হয় নিরক্ত বাক্যাবলী ‘অ্যাই বাবু, এগুলো করে না। আল্লাহ কি গোনাহ দিবে। ছোটবেলা থেকেই এইভাবে নৈতিকতার সাথে ধর্মের খিচুড়ি একসাথে মিশিয়ে এমনভাবে ছেলেমেয়েদের খাওয়ানো হয় যে তারা বড় হয়েও আর ভাবতেই পারে না যে ধর্ম মানা ছাড়াও কারো পক্ষে ভালো মানুষ হওয়া সম্ভব। কিন্তু সত্যিই কি ধর্মের সাথে নৈতিক চরিত্র গঠনের কোনো বাস্তব যোগাযোগ আছে? নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত, কৃষ্ণলীলা, তবলিগ জামাত ইত্যাদির মাধ্যমে গণমানুষের নৈতিকতা উন্নয়নের যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, পৃথিবী জুড়ে ধর্মের নামে মারামারি, হানাহানি, হিংসা, শোষণ, নির্যাতন, দারিদ্র্য আর সন্ত্রাসের বিস্তার দেখে বোঝা যায় যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস আসলে কোনো বিশাল অনুপ্রেরণা হয়ে মানুষের মধ্যে কথনোই কাজ করে নি। কারণটা অতি পরিষ্কার। ঈশ্বরে বিশ্বাসের মাধ্যমে মরালিটি বা নৈতিকতা অর্জনের চেষ্টা করা আসলে সোজা পথে ভাত না গিলে কানের চারিদিকে হাত ঘুরিযে ভাত খাওয়ার মতোন। প্রত্যেক ধর্মই বলছে বিধাতা ভালো মানুষকে পুরস্কৃত করেন আর পাপী তাপী-নীতিহীনদের শাস্তি দেন। বোঝাই যায়, পুরস্কারের লোভটাই এখানে মুখ্য নৈতিকতা বাদ দিয়ে অন্য যেকোনো উপায়ে আল্লাহকে তুষ্ট করে পুরস্কার লাভ করতে পারলে কোনো বান্দাই আর নৈতিকতার ধার ধারবে না। একটু ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে, রাম-নাম, হরিবোল, পাঁঠা বলি, কোরবানি, নামাজ, হজ, কোরআন তেলাওয়াত, পূজা, যজ্ঞ এই সমস্ত ব্যাপারগুলোর মাধ্যমে মানুষ আসলে নৈতিকতার কোনো ধার না ধেরে বিধাতার তুষ্টি লাভের প্রচেষ্টাতেই মত্ত। মানুষের প্রতি আর সমাজের প্রতি যাদের অবজ্ঞা আর প্রবঞ্চনা বেশি, তারাই কিন্তু বেশি-বেশি ‘আল্লা-আল্লা’ করে। মক্কা, জেরুজালেম, পুরী, বারানসি, তিরুপতি, এসব পবিত্র স্থান দর্শনে রয়েছে জীবনের সব পাপ ধুযে গিযে পরকালে স্বর্গবাসী হওয়ার নিশ্চিত গ্যারান্টি। কোটি টাকার চোরাকারবারি তাই ধুমধাম করে পূজা-যজ্ঞ করে নয়ত, শেষ বয়সে এলাকায় মন্দির/মসজিদ গড়ে দেয় স্বর্গে/বেহেশতে একটা প্লট বুকিং দেবার আশায়।
উপরন্তু, যুক্তি আর বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে সমাজ সচেতন মানুষ আজ বুঝতে শিখেছে যে, ঈশ্বর এক অর্থহীন অলীক কল্পনা মাত্র। রাহুল সাংকৃত্যায়নের ভাষায়-’অজ্ঞানতার অপর নামই হলো ঈশ্বর। কাজেই অজ্ঞানতাকে পুঁজি করে ঈশ্বর নামক মিথ্যা-বিশ্বাসের মুলা ঝুলিয়ে মানুষের নৈতিক চরিত্র গঠনের কাহিনি আজ অনেকের কাছেই শিশুতোষ ছড়া’ ছাড়া আর কিছু নয়। বার্ট্রান্ড রাসেল তার ‘হোয়াই আই অ্যাম নট আ খ্রিস্টান’ গ্রন্থে বলেন[২৫০]–
ধর্ম সম্পর্কে দু ধরনের আপত্তি করা যায়-বৌদ্ধিক এবং নৈতিক। বৌদ্ধিক আপত্তি অনুসারে বলা যায় যে, কোনো ধর্মকেই ধ্রুব সত্য বলে মেনে নেওয়ার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই এবং নৈতিক আপত্তি অনুসারে বলা যায় ধর্মের উপদেশগুলো এমন সময় থেকে উঠে এসেছিল যখন মানুষ বর্তমান যুগের থেকেও অনেক নিষ্ঠুর ছিল। ফলে দেখা যাচ্ছে এই উপদেশগুলো অমানবিকতাকে চিরন্তন করার জন্যই তৈরি। যদি এই চিরন্তন ব্যাপারটি গ্রহণে মানুষকে বাধ্য না করা হতো, তবে মানুষের নৈতিক বিবেকবোধ বর্তমানে আরও অনেক উন্নত হতো।
এই বইয়ের লেখকদ্বয়ের দুজনেরই ইন্টারনেটে ধার্মিকদের নানা (কু) যুক্তির সাথে পরিচয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। একবার এক ওযেবসাইটের জন্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্ম এবং নৈতিকতার মধ্যকার বিভিন্ন অসংগতি নিয়ে লেখা শুরু করেছিলাম। লেখা শুরু করতে না করতেই এক ধার্মিক ভদ্রলোক সেখানে হুঙ্কার ছেড়ে তেড়ে আসলেন এই বলে–
এদের মতো ব্যক্তিবর্গ যুগ যুগ ধরে এসেছে এবং ভূত হয়ে চলে গেছে। এদের সম্পর্কে কোরআনে উল্লেখ রয়েছে যে, তারা অন্ধ ও বর্বর। এদের হৃদয়ে সীলমোহর এঁটে দেওয়া আছে। তারা কিছুই দেখতে পায় না এবং শুনতে পায় না। শুধু প্রাণীর মতো হাম্বা হাম্বা রব তোলে।
কোরআনে যদি সত্যিই এমনটি বলা থাকে (এবং কোরআনে সত্যিই অবিশ্বাসীদের অন্ধ/বর্বর, এবং এদের হৃদয়ে যে সীলমোহর এঁটে দেওয়া আছে তা বলা আছে; দেখুন সুরা ২ : ৭, ৪ : ১৫৫, ৭ : ১০০, ৭: ১০১, ৯ : ৯৩, ১৬ : ১০৮, ৩০ : ৫৯, ৪৫ : ২৩ ইত্যাদি) বলতেই হয় মহান সৃষ্টিকর্তার রুচিবোধ সত্যিই প্রশংসনীয়। কেবল ধর্ম মানি না বলেই ভদ্রলোক আমাদের ‘অন্ধ’ ও ‘বর্বর’ বলেছেন, আর প্রমাণ স্বরূপ ‘সাক্ষী গোপাল’ মেনেছেন তার চির-আরাধ্য ওই ধর্মগ্রন্থকেই। শুধু যে কোরআনেই অধার্মিকদের সম্বন্ধে এধরনের বিষোদগার করা হয়েছে তা ভাবলে ভুল হবে। শঙ্করাচার্য প্রমুখ দার্শনিকদের প্রাচীনকালের নাস্তিক্যবাদী চার্বাক দর্শনকে লোকায়ত বা ইতর লোকের দর্শন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার প্রবণতাটির কথা এক্ষেত্রে বিবেচনা করা যেতেই পারে। এমনকি চার্বাক দর্শনের উৎপত্তি সম্বন্ধেও বলা হয় যে, মহাভারতের এক কুচরিত্র রাক্ষস চার্বাকের নাম থেকেই নাকি চার্বাক দর্শনের উৎপত্তি হয়েছে। মহাভারতে আছে, চার্বাক ছিল দুর্যোধনের বন্ধু এক দুরাত্মা রাক্ষস। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জযের পর চার্বাক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ ধারণ করে যুধিষ্ঠিরকে জ্ঞাতিঘাতী হিসেবে ধিক্কার জানিয়ে আত্মঘাতী হতে প্ররোচিত করেছিল। কিন্তু উপস্থিত ব্রাহ্মণেরা তাদের অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় চার্বাকের চালাকি ধরে ফেলে যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করেন। বোঝাই যায়, প্রাচীন ভাববাদীরা এই নাস্তিক্যবাদী দর্শনটির প্রতি সাধারণ মানুষের ঘৃণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই এমন ঘৃণ্য চরিত্রের রাক্ষসের সাথে দর্শনটিকে জুড়ে দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। আরেকটি উদাহরণ দেখি।
মহাভারতের শান্তিপর্ব। এক ধনী বণিক রথে যাওয়ার সময় এক ব্রাহ্মণকে ধাক্কা মেরে দিল। ক্ষুব্ধ ব্রাহ্মণ অপমানের জ্বালা ভুলতে আত্মহত্যা করার কথা চিন্তা করল। দেবরাজ ইন্দ্র ব্রাহ্মণের আত্মহত্যার মধ্যে সর্বনাশের সঙ্কেত দেখতে পেয়ে শিয়াল সেজে হাজির হলেন। ব্রাহ্মণকে তার পশু জীবনের নানা দুঃখ-দুর্দশার কথা বলে মানবজীবনের জয়গান গাইলেন। জানালেন অনেক জন্মের পুণ্যের ফল সম্বল করে এই মানব জন্ম পাওয়া। এমন মহার্ঘ্যতম এই মানবজীবন আর তার ওপর আবার ব্রাহ্মণ! এমন জীবন পাওয়ার পরও কি কেউ আত্মহত্যা করে? কাজেই অভিমানে আত্মহত্যা করা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। শিয়াল বলল, সে নিজেও আগের জন্মে ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছিল। কিন্তু সেই জন্মে সে চুড়ান্ত মূর্খের মতো এক মহাপাতকের কাজ করেছিল বলেই আজ এই শিয়াল জন্ম। চুড়ান্ত মূর্খের মতো কাজটি কী? এ বারেই কিন্তু বেরিয়ে এলো নীতি কথা–
অহমাংস পণ্ডিতকো হৈতুকো দেবনিকঃ
আম্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যম্ অনুরক্তো নিরার্থিকাম।
হেতুবাদা প্রবদিতা বক্তা সুংসৎসু হেতুমৎ।
আক্রোষ্টা চ অভিবক্তা চ ব্রাহ্মবাক্যেষু চ দ্বিজা।।
নাস্তিকঃ সর্বশঙ্কী চ মূৰ্থঃ পণ্ডিতমানিকঃ
ভাস্য ইয়ং ফলনিবৃত্তিঃ শৃগালত্বং মম দ্বিজ (শান্তিপর্ব ১৪০/৪৭-৪৯)।
(অর্থাৎ, আমি ছিলাম এক বেদ সমালোচক পণ্ডিত। নিরর্থক তর্কবিদ্যায় ছিলাম অনুরক্ত বিচার সভায় ছিলাম তর্কবিদ্যার প্রবক্তাযুক্তিবলে দ্বিজদের ব্রহ্মবিদ্যার বিরুদ্ধে আক্রোশ মেটাতাম। ছিলাম জিজ্ঞাসু মনের নাস্তিক, অর্থাৎ কিনা পণ্ডিতাভিমানী মূর্খ। হে ব্রাহ্মণ, তারই ফলস্বরূপ আমার এই শিয়াল জন্মা)।
বোঝাই যায়, বৈদিক যুগেও যুক্তিবাদীদের সংশয়, অযাচিত প্রশ্ন আর অনর্থক তর্ক-বিতর্ক একটা ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছিল। ‘পণ্ডিতাভিমানী মূৰ্থ-এধরনের লেবেল এঁটে দিয়ে বেদ-সমালোচকদের প্রতিহত করার প্রচেষ্টা তারই ইঙ্গিত বহন করে। আজকেও কি এ দৃষ্টিভঙ্গির খুব একটা পরিবর্তন হয়েছে? যে ভদ্রলোকটি ধর্মগ্রন্থের সমালোচনা করার জন্য আমাদের ‘অন্ধ’ বা ‘বর্বর হিসেবে চিত্রিত করছেন, সে ধরনের লোকজনের কিন্তু আজও সমাজে অভাব নেই, নাস্তিক শুনলেই তারা চিৎকার করে ওঠেন ‘ও তুমি নাস্তিক! তবে তো তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারো! তোমার তো চরিত্র বলে কিছু নেই। এরা আসলে নাস্তিকদের মানুষ বলেই মনে করেন না, ভালো-মানুষ ভাবা তো অনেক পরের কথা। কিন্তু, নাস্তিক মানেই কি অনৈতিক, চরিত্রহীন, লম্পট গোছের কিছু? এমনই ভাবে ভাবার মোটেই কোনো কারণ নেই। নাস্তিকরা আসলে নাকের সামনে থেকে ঈশ্বর নামক মুলাটি সরিয়ে বাস্তবসম্মতভাবে ‘মরালিটি বা নৈতিকতাকে দেখার পক্ষপাতী। ঈশ্বরের ভয়ে নয়, একটি সুন্দর এবং সুস্থ সমাজ গড়ে তুলার প্রযোজনেই মানুষের চুরি, লাম্পট্য, খুন, ধর্ষণ বিসর্জন দিয়ে সামাজিক মূল্যবোধগুলো গড়ে তোলা দরকার। নয়ত সমাজের ভিত্তিমূলই যে একসময় ধ্বসে পড়বে! কাজেই অধার্মিকদের চোখে ‘নৈতিকতা বেহেস্তে যাওয়ার কোনো পাসপোর্ট নয়, বরং নিতান্তই সামাজিক আবশ্যকতা। ধর্মান্ধরা যেহেতু সামাজিক মূল্যবোধের এই বিষয়গুলো একেবারেই বুঝতে চান না, তাই তাদের মধ্যে যুদ্ধ, দাঙ্গা, জিহাদ, মারামারি লেগেই আছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের কথাই ধরা যাক। সারা বাংলা হতবিহ্বল হয়ে দেখেছে কিছু ধর্মান্ধ মানুষ ধর্ম রক্ষা করার নামে কী করে পশুর স্তরে নেমে যেতে পারে।
এক ভদ্রলোককে চিনতাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাতে-পাঁচে নেই; সাদা চোখে দেখলে নিতান্ত ভালোমানুষ বলেই মনে হবে। কিন্তু ভুক্তভোগীরা জানেন যে একাত্তরে ভদ্রলোক এহেন দুষ্কর্ম নেই যে করেন নি। সেসময় এমনকি তিনি ফতোয়া দিয়েছিলেন এই বলে যে, খান-সেনারা যদি কোনো বাঙালি মেয়েকে ধর্ষণ করে তবে সেটি অন্যায় বলে বিবেচিত হবে না, বঙ্গনারীরা পাক-বাহিনীর জন্য মালে গনিমত’, কারণ তারা ইসলামের জন্য লড়ছে। এমন নয় যে ভদ্রলোক মূর্খ ছিলেন, অথবা ছিলেন বুদ্ধিহীন। বরং সৎ এবং হৃদযবান হিসেবেই একটা সময় তার খ্যাতি ছিল; কিন্তু এই আপাতদৃষ্টিতে ‘সজ্জন ব্যক্তিও স্রেফ ধর্মের প্রতি ভালোবাসায় অন্ধ হয়ে নেমে গেলেন পশুর স্তরে উনি ভেবেছিলেন পাকিস্তান ভেঙে গেলে ইসলাম হবে বিপন্ন। তাই ধর্ম বাঁচাতে যা যা করা দরকার সবই করেছেন। এমনকি খান সেনাদের সাথে পাল্লা দিয়ে তার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগও আছে। ব্যাপারটি অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও অতিমাত্রায় ধর্মপ্রবণদের জন্য এধরনের কাজ খুবই স্বাভাবিক। অনেক সময়ই মানবিকতার চেয়ে তাদের কাছে ধর্মবোধটাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। এই ভদ্রলোকের কথা ভাবলেই নোবেল বিজয়ী পদার্থবিদ স্টিফেন ওয়াইনবার্গের বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়ে যায়[২৫১]–
ধর্ম মানবতার জন্য এক নির্মম পরিহাস। ধর্ম মানুক বা নাই মানুক, সবসময়ই এমন অবস্থা থাকবে যে ভালো। মানুষেরা ভালো কাজ করছে, আর খারাপ মানুষেরা। খারাপ কাজ করছে। কিন্তু ভালো মানুষকে দিয়ে খারাপ কাজ করানোর ক্ষেত্রে ধর্মের জুড়ি নেই।
শুধু একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধই তো কেবল নয়, বছর কয়েক আগে গুজরাটে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক দাঙ্গা, আর তারও আগে অযোদ্ধা বাবরি মসজিদ ভেঙে শিবসেনাদের তাণ্ডব নৃত্য ধর্মের এই ভয়াবহ রূপটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। অপরপক্ষে নাস্তিকদের যেহেতু এই অতিমানবিক সত্ত্বা-কেন্দ্রিক নৈতিকতায় কোনো বিশ্বাস নেই, ফলে একজন নিষ্ঠাবান নাস্তিক সত্যিকার অর্থে গড়ে উঠতে পারেন একজন যথার্থ প্রথা-বিরোধী মানুষ হিসেবে। সুমন তুরহান নামে এক লেখক মাসিক দেশ পত্রিকার ৪ নভেম্বর ২০০২ সংখ্যায় ‘নাস্তিকতার সংজ্ঞা’ শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছিলেন[২৫২]– ‘নাস্তিকদের অবিশ্বাস তাই শুধু অতিমানবিক সত্বায় নয়, তারচেয়ে অনেক গভীরে, তিনি অবিশ্বাস করেন প্রথাগত সভ্যতার প্রায় সমস্ত অপবিশ্বাসে। সবকিছুই তারা যুক্তি দিয়ে বিচার করে দেখতে চান। এর মধ্যে কিছুটা হলেও যে সত্যতা নেই তা নয়। তবে ভালোমানুষ হোন, আর নাই হোন এটা কিন্তু ঠিক যে নাস্তিক বা অধার্মিকদের মধ্যে থেকে কখনোই আল-কায়েদা, তালিবান, হরকত-উল-জিহাদ, রাজাকার, আলবদর বা শিবসেনাদের মতো সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক রূপ দেখা যায় না। যতদিন ধর্ম থাকবে, ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকবে ধর্মের সাম্প্রদায়িক এই সাংগঠনিক রূপটিও কিন্তু বজায় থাকবে পুরোমাত্রায়। কাজেই যতদিন মানুষের আনুগত্য ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে বিভক্ত হয়ে থাকবে ততদিন তা মানুষকে স্বাধীনভাবে আর বিজ্ঞানসম্মতভাবে নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অর্জনে বাধা দেবেই। বেহেস্তের লোভে বা ঈশ্বরকে তুষ্ট করার জন্য নয়, মানুষকে ভালোবেসে মানুষের জন্য কাজ করার প্রচেষ্টা যদি আন্তরিক হয়, তবেই গড়ে উঠবে সর্বজনীন মানবতাবাদ। সম্প্রতি এর প্রচেষ্টা শুরুও হয়েছে। ঈশ্বরকেন্দ্রিক মিথ্যার বেসাতি মন থেকে সরিযে শুধু মানুষের জন্য মানুষের কাজ করার বাসনা নিয়ে পৃথিবী জুডে নতুন শতকের আধুনিক মতবাদ হিসেবে এসেছে হিউম্যানিজম। এমনকি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে মানবতাবাদী সমিতি এবং যুক্তিবাদী সমিতি অফিস আদালতের ফর্মে বা বিয়ের রেজিস্ট্রেশনে ‘হিন্দু, মুসলিম এই শব্দগুলোর পাশাপাশি ধর্মের জায়গায় মনুষ্যত্ব’ শব্দটি ব্যবহারের আইনি অধিকার আদায় করেছে[২৫৩]। এ প্রসঙ্গে ভারতীয় যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষের একটি চমৎকার উক্তি তার ‘অলৌকিক নয়, লৌকিক (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থ থেকে হুবহু তুলে দিচ্ছি[২৫৪]–
আগুনের ধর্ম যেমন দহন, ছুরির ধর্ম যেমন তীক্ষ্ণতা তেমনই মানুষের ধর্ম হওয়া উচিত মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধন। আর সে হিসেবে নামাজ না পড়েও বা শনি শীতলার পূজা না করেও আমরা যুক্তিবাদী নাস্তিকেরাই প্রকৃত ধার্মিক, কারণ আমরা মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ চাই।
.
ধর্মগ্রন্থগুলো কি সত্যিই নৈতিকতার ধারক এবং বাহক?
ইদানীং এক নতুন ধরনের প্রগতিবাদী (নাকি সুবিধাবাদী?) আন্দোলন শুরু হয়েছে, যার মূলমন্ত্র হলো ধর্ম নয়, কেবল মৌলবাদকে আঘাত করো। এমনকি মুক্তমনা যুক্তিবাদীদেরও অনেকে দেখছি বুঝে হোক, না বুঝে হোক এ প্রচারণায় গা ভাসিয়ে দিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের মতোই সোচ্চারে বলছেন : শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও মৌলবাদ রুথব’, যেন মৌলবাদ ব্যাপারটি হঠাৎ করেই আকাশ থেকে আবির্ভূত হয়েছে মহীরুহ আকারে-কোনো শিকড়-বাকড় ছাড়াই। যারা ধর্মকে শাশ্বত চিরন্তন আর জনকল্যাণমূলক বলে মনে করেন আর যত দোষ চাপাতে চান কেবল ওসামা বিন লাদেন, গোলাম আজম, আদভানী কিংবা মৌলবাদ’ নামক নন্দঘোষটির ঘাড়ে, তাদের প্রথমে খোদ ‘মৌলবাদ’ শব্দটিকেই বিশ্লেষণ করে দেখতে বলি। মৌল’ শব্দের অর্থ মূল থেকে আগত, বা ‘মূল সম্বন্ধীয়’ আর ‘বাদ’ শব্দের অর্থ যে মত’, ‘তত্ব’ বা ‘থিওরি’, তা তো আমরা জানিই। তা হলে ‘মৌলবাদ’ শব্দের প্রকৃত অর্থ কী দাঁড়ালো? দাঁড়ালো-মূল থেকে আগত তত্ব। কোন মূল থেকে আগত তত্ব? শেষ পর্যন্ত ওই ধর্মগ্রন্থের গোঁড়া মূলনীতিগুলো হতে আগত তত্ব। কাজেই বিচার-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কিন্তু থলের বিড়াল ঠিকই বেরিয়ে পড়ছে যে, ধর্মশাস্ত্রের মূলনীতিগুলোকে চরম সত্য বলে যারা মনে করেন, তারাই শেষ পর্যন্ত মৌলবাদী হন। মৌলবাদ শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো ‘Fundamentalism’। এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে বলা হয়েছে– ‘Strict maintenance of traditional scriptural beliefs”; চেম্বার্স ডিকশনারি শব্দটি সম্পর্কে বলছে ‘Belief in literal truth in Bible, against evolution etc.’। কাজেই ধর্মকে বাদ দিয়ে মৌলবাদ রুখবার চেষ্টা অনেকটা বিষবৃক্ষের মূলে পানি ঢেলে তাকে বাঁচিয়ে রেখে আগায় কাঁচি চালানোর প্রচেষ্টা, নিছক ভণ্ডামি। প্রসঙ্গত দেশ থেকে নির্বাসিত হবার পর তসলিমা নাসরিন একবার একটি ইংরেজি পত্রিকার সাথে সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন[২৫৫]–
আমি সাধারণভাবে মৌলবাদীদের আর সেইসাথে ধর্মের দুরেই সমালোচনা করেছিলাম। আমি আসলে ইসলামের সাথে ইসলামি মৌলবাদের কোনো তফাৎ দেখি না। আমি মনে করি ধর্মই হচ্ছে মূল উৎস, যেটি থেকে মৌলবাদ নামক বিষাক্ত ডালপালাগুলো সময় সময় বিস্তার লাভ করে। যদি আমরা ধর্মকে অক্ষত রেখে দেই, কেবল মৌলবাদ নামক একটি ডালকে হেঁটে ফেলতে সচেষ্ট হই, দেখা যাবে কিছু দিন পর মৌলবাদের আরেকটা শাখা। অচিরেই বেড়ে উঠেছে। আমি খুব পরিষ্কারভাবেই এটি বলছি কারণ, কিছু উদারপন্থী লোকজন আছেন যারা এধরনের প্রশ্নে ইসলামকে ডিফেন্ড করেন আর সমস্ত সমস্যার জন্য কেবল মৌলবাদীদের ঘাড়ে দোষ চাপিযে দিয়ে ক্ষান্ত হন। কিন্তু ইসলাম নিজেই তো নারী নির্যাতনকারী। ইসলাম নিজেই তো গণতন্ত্র সমর্থন করে না আর সমস্ত মানবিক অধিকার হরণ করে।
আমাদের এক পরিচিতজন আছেন-সেকুলার এবং প্রগতিশীলতার দাবিদার। কিন্তু তসলিমার এই সাক্ষাৎকার পড়ে তার যেন পিত্তি জ্বলে গেল! তসলিমা ‘শ্যালো’, তসলিমা ‘নির্বোধ’, তসলিমা ‘ইডিয়ট’, কী নন তিনি! বুঝলাম, তসলিমার বড় অপরাধ তিনি ধর্ম আর মৌলবাদকে এক করে ফেলেছেন। কিন্তু তসলিমা ভুল বলছেন না ঠিক বলছেন সেটি বিশ্লেষণ করতে হলে নির্মোহ সংশয়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মগ্রন্থগুলোর দিকে তাকানো দরকার। আসুন প্রিয় পাঠক, আমরা যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে দেখি-ধর্মগ্রন্থগুলোর সাথে মৌলবাদের সত্যিই কোনো প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে কিনা এবং ধর্মগ্রন্থগুলো আদপেই নৈতিকতার ভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত হওয়ার যোগ্যতা রাখে কিনা!
.
ধর্মগ্রন্থগুলো আসলে কী বলছে?
পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্মমতগুলো সৃষ্টি হয়েছে বড়জোর বিগত ২-৪ হাজার বছরের মধ্যে। হিন্দু, ইসলাম কিংবা খ্রিস্ট ধর্ম কোনোটাই সে অর্থে চিরন্তন বা সনাতন নয়। কাজেই ‘সনাতন ধর্ম নিছকই একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস। তবে সনাতন না হলেও ধর্ম সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু কিন্তু হয়েছিল বহু হাজার বছর আগে। বিরূপ প্রকৃতির নানা দুর্যোগ দাবানল, প্লাবন, বজ্রপাত প্রভৃতির ব্যাখ্যা খুঁজতে অসহায় হয়ে আর ওগুলোর হাত থেকে মুক্তি খুঁজতে মানুষ সৃষ্টি করেছিল নানা দেব-দেবীর; মৃত্যুকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা না করতে পেরে সৃষ্টি করেছিল অদৃশ্য আত্মার। যারা সমাজ বিজ্ঞান নিয়ে সামান্য পড়াশোনা করেছেন তারাই এগুলো জানেন। আর এখন পর্যন্ত জানা তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায়, মানুষের মধ্যে তথাকথিত ‘ধর্মবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিল নিয়ান্ডার্থাল মানুষের আমলে-যারা পৃথিবীতে রাজত্ব করেছে এখন থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ বছর আগে। নিয়ান্ডার্থাল মানুষের আগে পিথেকানথ্রোপাস আর সিনানথ্রোপাসদের মধ্যে ধর্মাচরণের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নি। তবে নিয়ান্ডার্থাল মানুষের বিশ্বাসগুলো ছিল একেবারেই আদিম-আজকের দিনের প্রচলিত ধর্মমতগুলোর তুলনায় একেবারেই আলাদা। এখন থেকে ৪০-১৫ হাজার বছর আগে উচ্চতর পুরা-প্রস্তর যুগে। এসে আত্মা, পরমাত্মা, ধর্মীয় আচার আর জাদুবিদ্যা সংক্রান্ত ব্যাপার-স্যাপারগুলো সুসংহত হয়। আজকের দিনের ধর্মবিশ্বাসগুলোর মধ্যে বৈদিক ধর্মের (হিন্দু ধর্মের পূর্বসূরি) উদ্ভব হয়েছিল আজ থেকে মাত্র ৩৫০০ বছর আগে, ইসলাম ধর্ম এসেছে ১৪০০ বছর আগে, খ্রিস্টধর্ম ২০০০ বছর আগে, ইত্যাদি। একটা সময় সামাজিক প্রয়োজনে যে ধর্মীয় রীতিনীতি নিয়ম কানুন তৈরি হয়েছিল, আজ তার অনেকগুলোই কালের পরিক্রমায় স্থবির, পশ্চাৎপদ, নিবর্তনমূলক এবং অমানবিক বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ইতিহাস পরিক্রমায় দেখা যায় ফোনিকান, হিব্রু, ক্যানানাইট, মায়া, ইনকা, অ্যাজটেক, ওলমেক্স, গ্রিক, রোমান কার্যাগিনিত্যান, টিউটন, সেল্ট, ভুইড, গল, থাই, জাপানি, মাউরি, তাহিতিয়ান, হাওয়াই অধিবাসী-সবাই নিজ নিজ ধর্ম অনুযায়ী নির্বিচারে শিশু, নারী, পুরুষ বলি দিয়েছে তাদের অদৃশ্য দেব-দেবীদের তুষ্ট করতে। এই বইয়ের পরবর্তী ‘বিশ্বাসের ভাইরাস অধ্যায়টিতে এ নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব। এই অধ্যায়ে আমরা কেবল প্রচলিত এবং গুরুত্বপূর্ণ ধর্মমতগুলোর ঐশী ধর্মগ্রন্থগুলোতে চোখ রাখব; আমরা নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব, ধর্মগ্রন্থগুলো আসলে কী বলছে।
যারা কোরআন আগাগোড়া পড়েছেন তারা সকলেই জানেন, পবিত্র কোরআনের বেশ অনেকটা জুড়েই রয়েছে উত্তেজক নির্দেশাবলী। যেমন[২৫৬]–
যেখানেই অবিশ্বাসীদের পাওয়া যাক তাদের হত্যা করতে (২: ১৯১, ৯ : ৫), তাদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হতে, কঠোর ব্যবহার করতে (৯ : ১২৩), আর যুদ্ধ করে যেতে (৮ : ৬৫)। বিধর্মীদের অপদস্থ করতে আর তাদের ওপর জিজিয়া কর আরোপ করতে (৯ : ২৯)। অন্য সকল ধর্মের অনুসারীদের কাছ থেকে ধর্মীয় স্বাধীনতার নির্যাসটুকু কেড়ে নিয়ে সোচ্চারে ঘোষণা করছে যে, ইসলামই হচ্ছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম (৩ : ৮৫)। এটি অবিশ্বাসীদের দোজখে নির্বাসিত করে (৫ : ১০), এবং ‘অপবিত্র’ বলে সম্বোধন করে (৯ : ২৮); মুসলিমদের ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আদেশ করে যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য সকল ধর্মকে সরিয়ে ইসলামি রাজত্ব কায়েম হয় (২: ১৯৩)। কোরআন বলছে যে শুধু ইসলামে অবিশ্বাসের কারণেই একটি মানুষ দোজখের আগুনে পুড়বে আর তাকে সেখানে পান করতে হবে দুর্গন্ধময় পুঁজ (১৪ : ১৭)। অবিশ্বাসীদের হত্যা করতে অথবা তাদের হাত-পা কেটে ফেলতে প্ররোচিত করছে, দেশ থেকে অপমান করে নির্বাসিত করতে বলছে-’তাদের জন্য পরকালে অপেক্ষা করছে ভয়ানক শাস্তি’ (৫ : ৩৪)। আরও বলছে, যারা অবিশ্বাস করে তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে আগুনের পোশাক, তাদের মাথার ওপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে যাতে ওদের চামড়া আর পেটে যা আছে তা গলে যায়, আর ওদের পেটানোর জন্য থাকবে লোহার মুগুর’ (২২ : ১৯)। কোরআন ইহুদি এবং নাসারাদের সাথে বন্ধুত্বটুকু করতে পর্যন্ত নিষেধ করছে (৫ : ৫১), এমনকি নিজের পিতা বা ভাই যদি। অবিশ্বাসী হয় তাদের সাথে সম্পর্ক না রাখতে উদ্বুদ্ধ করছে (৯ : ২৩, ৩ : ২৮)T আল্লা-রসুলে যাদের বিশ্বাস নেই, তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড (৪৮ : ১৩)। ইসলামে অবিশ্বাস করে কেউ। মারা গেলে কঠোরভাবে উচ্চারিত হবে ‘ধরো ওকে, গলায় বেড়ি পড়াও এবং নিক্ষেপ করো জাহান্নামে আর তাকে শৃঙ্খলিত করো সত্তর হাত দীর্ঘ এক শৃঙ্খলে’ (৬৯ : ৩০ ৩৩)। আল্লাহর নামে যুদ্ধ করতে সবাইকে উৎসাহিত করা হয়েছে এই বলে এটা আমাদের জন্য ভালোই, এমনকি যদি আমাদের অপছন্দ হয় তবুও (২ : ২১৬), তারপর ‘কাফেরদের গর্দানে আঘাত করো’ আর তারপর তাদের ওপর রক্তগঙ্গা বইয়ে দেওয়ার নির্দেশের পর রয়েছে অবশিষ্টদের ভালোভাবে বেঁধে ফেলতে (৪৭ : ৪)। আল্লাহতালা এই বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন ‘কাফেরদের। হৃদয়ে আমি গভীর ভীতির সঞ্চার করব’ এবং বিশ্বাসীদের আদেশ করেছেন কাফেরদের কাঁধে আঘাত করতে আর হাতের সমস্ত আঙুলের ডগা ভেঙে দিতে (৮ : ১২)
আল্লাহ জিহাদকে মুমিনদের জন্য আবশ্যক (mandatory) করেছেন আর সতর্ক করেছেন এই বলে তোমরা যদি সামনে না এগিয়ে আসো (জিহাদের জন্য) তবে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে মর্মন্তুদ শাস্তি’(৯ : ৩৯)। আল্লাহ তার পেয়ারা নবীকে বলছেন, ‘হে নবী, অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করো আর কঠোর হও কেননা, জাহান্নামের মতো নিকৃষ্ট আবাস স্থলই হলো তাদের পরিণাম’ (৯ : ৭৩)।
এই হচ্ছে কোরআন (হাদিস এবং অন্যান্য গ্রন্থগুলোর কথা না হয় বাদই থাকুক আপাতত)। অনেকেই দেখেছি নিজস্ব বিশ্বাসে আপ্লুত হয়ে কোরআনকে নির্দ্বিধায় ‘The book of guidance’ বলে মেনে নেন, আর ইসলামকে মনে করেন ‘শান্তির ধর্ম। যারা এমনটি ভাবেন, তারা কি কখনও ভেবে দেখেছেন যে উপরের আয়াতগুলো কেউ যদি নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করে আর সমাজে তার বাস্তব প্রয়োগ চায় তবে তারা কী ধরনের শান্তি এ পৃথিবীতে বয়ে আনবে? জিহাদিদের কল্যাণে আজকের বিশ্বে ‘ইসলামি সন্ত্রাসবাদ’ (Islamic Terrorism) একটি প্রতিষ্ঠিত শব্দ। প্রতিদিন কাগজের পাতা খুললেই দেখা যায় এই জিহাদি জোশে উদ্বুদ্ধ কিছু লোক বোমা মারছে মানুষজন, বাড়ি-ঘর, কারখানা, রাস্তাঘাট, যানবাহন, সিনেমা হল, সাংস্কৃতিক অঙ্গন বা সমুদ্র-সৈকতে। হাজার খানেক জিহাদি সংগঠন যেমন-আল কায়দা, ইসলামিক জিহাদ, হামাস, হরকত-উল-জিহাদ, হরকত-উল-মুজাহিদিন, জেইস-মুহম্মদ, জিহাদ-এ-মুহম্মদ, তাহ-রিখ-এ-নিফাজ সারিয়াত-এ-মুহম্মদ, আল-হিকমা, আল-বদর মুজাহিদিন, জামাতে ইসলামিয়া, হিজাব-এ-ইসলামিয়া আজ সারা পৃথিবীতে কাযেম করছে এক ভীতির পরিবেশ[২৫৭]–
বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি (২৩ অক্টোবর, ২০০৯) নিষিদ্ধ করে হিযবুত তাহরীরকে জঙ্গিবাদের অভিযোগে। এর আগে বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের আমলে জমিয়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি), হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামি বাংলাদেশ (হুজি) নিষিদ্ধ হয়; শাহাদাত ই আল হিকমা ও জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি) নিষিদ্ধ হয় চারদলীয় জোট সরকারের আমলে। বাংলাদেশে হরকাতুল জিহাদ প্রথম আলোচনায় আসে ১৯৯৬ সালে। ওই বছর ১৯ ফেব্রুয়ারি কক্সবাজার জেলার উখিয়া থানার পাইনখালী গ্রামসংলগ্ন লুন্ডাখালীর জঙ্গলে সেনাবাহিনী ও পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে সশস্ত্র প্রশিক্ষণের সময় ঐ সংগঠনের ৪১ জঙ্গি সদস্যকে অস্ত্র-গোলাবারুদসহ গ্রেফতার করে। ওই ৪১ জনের মধ্যে একজন বিদেশি নাগরিক ছাড়া বাকিরা ছিল দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসা মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষক। এরপর ১৯৯৯ সালের ১৮ জানুয়ারি ঢাকায় কবি শামসুর রাহমানের বাড়িতে তার ওপর হামলাকালে ঘটনাস্থল এবং পরে বিভিন্ন স্থান থেকে আটক ১০ জঙ্গিও নিজেদের হরকাতুল জিহাদের সদস্য পরিচয় দেয়। এরপর যশোরে উদীচীর অনুষ্ঠানে, ২০০০ সালের ২৩ জুলাই গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়ায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জনসভার অদূরে বোমা পুঁতে রাখার ঘটনায়, এরপর ২০০১ সালের ১৪ এপ্রিল রমনার বটমূলে নববর্ষের অনুষ্ঠানে, ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা এবং ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট সিরিজ। বোমা হামলাসহ সারা দেশে বেশকিছু বোমা, গ্রেনেড হামলা চালিয়ে হরকাতুল জিহাদ আবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আসে।
১৯৯৮ সালে জন্ম নেওয়া জেএমবি ২০০২ সাল থেকে নাশকতা শুরু করলেও ব্যাপক আলোচনায় আসে ২০০৫ সালের ১৭ আগস্ট দেশব্যাপী একযোগে বোমা হামলা চালিয়ে। পাঠকদের অনেকেরই হয়ত সেদিনকার ভয়াবহতার কথা মনে আছে। সেদিন সারা বাংলাদেশে একনাগাড়ে ৬৩টি জেলায় বোমার মহড়া চালিয়েছিল। মহড়ার প্রকোপ এমনই ব্যাপক ছিল যে অনেকেই ১৭ই আগস্ট দিনটিকে সেসময় বাংলাদেশের ৯/১১’ বলে অভিহিত করেছিলেন। জঙ্গিবাদের সাথে বিশুদ্ধ ইসলামের সম্পর্ক কতটুকু তা বোঝা হয়ে গেছে বোমা মহড়ার স্থানগুলোতে পাওয়া তাদের ছাপানো লিফলেটগুলো থেকেই। লিফলেট জুড়ে কোরআন-হাদিস থেকে নানা উদ্ধৃতি আর কাফের নাফরমানদের বিরুদ্ধে জিহাদের ডাক দেওয়া হয়। সেসময় ফরহাদ মজহার আর বদরুদ্দীন উমরেরা পালের হাওয়া অন্য দিকে ঘোরানোর চেষ্টা করলেও, বিশুদ্ধ ইসলামের সাথে জঙ্গিবাদের যে একটা সম্পর্ক রয়েছে, তা আর চাপা থাকে নি। ধর্মভিত্তিক ৫টি জঙ্গি সংগঠনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ হলেও ইতোমধ্যে গোপনে আরও ৭০টি জঙ্গি সংগঠন এদের সাথে যুক্ত হয়েছে। এরা একযোগে গোপনে দেশব্যাপী বড় ধরনের নাশকতা ঘটানোর জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। শাহবাগ আন্দোলনের সময় নাস্তিক ব্লগারদের খুঁজে খুঁজে হত্যার জন্য গঠিত আনসারউল্লাহ বাংলা টিমের কীর্তিকলাপের কথাও পত্রিকায় এসেছে। এদের মূল টার্গেট হচ্ছে আসলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বানচাল করা[২৫৮]।
সচেতন শান্তিকামী ধার্মিক মানুষদের আজ আত্মােপলব্ধির সময় এসেছে, সময় এসেছে সংশয়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন করার-কেন এই জঙ্গি দুলগুলো এত ইসলামিক? কেন তারা সন্ত্রাসী? কারা ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছে মোল্লা ওমর, বিন-লাদেন, মৌলানা মান্নান, গোলাম আজম, শাইখ আব্দুর রহমান, মুফতি হান্নান আর বাংলা ভাইদের? কে ইন্ধন যোগায় তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে? আজ অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে তাই বলার সময় এসেছে-এই তথাকথিত ‘পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলো অনেকাংশেই ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের মূল উৎস। তবে সেইসাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা দেশগুলোর সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং মধ্যপ্রাচ্যের প্রতি দীর্ঘদিনের বিদ্বেষমূলক পররাষ্ট্রনীতির কথাও আমাদের ভুলে গেলে চলবে না[২৫৯]। জন-বিধ্বংসী যুদ্ধাস্ত্র না পাওয়া কিংবা সাদ্দামের সাথে আল-কায়েদার কোনো সম্পর্ক না খুঁজে পাওয়া কিংবা জৈব-যুদ্ধাস্ত্র না পাওয়া সত্বেও নির্লজ্জভাবে ইরাকের ওপর যে আগ্রাসন চালিয়েছে তা শুধু যে আমেরিকার চিরচেনা সাম্রাজ্যবাদী চেহারাটাকেই স্পষ্ট করে তুলেছে তা নয়, ইসলামি বিশ্ব এই আগ্রাসনকে যেকোনো কারণেই হোক ‘ইসলামের ওপর আঘাত’ হিসেবে নিয়েছে। সেজন্য রাজনৈতিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, সেসমস্ত দেশেই ইসলামি আত্মঘাতী বোমা হামলার মাত্রাটা বেশি যে দেশের সরকার ইরাক যুদ্ধে বুশ-ব্লেয়ারকে নগ্নভাবে সমর্থন করেছে। প্যালেস্টাইনদের বঞ্চিত করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলো যেভাবে দীর্ঘদিন ধরে ইসরায়েলকে নগ্নভাবে সমর্থন করেছে তাও মুসলিম সমাজকে সংঘাতের পথে ঠেলে দিয়েছে। এই রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া আর প্রতিহিংসার ব্যাপারগুলো ভুলে গেলে কোনো আলোচনাই কখনও সম্পূর্ণ হতে পারে না। আরেকটি ব্যাপার উল্লেখ করাও বোধহয় এক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রাষ্ট্রযন্ত্র কীভাবে ধর্ম ও মৌলবাদকে লালন করে, পালন করে আর সময় বিশেষে উস্কে দেয় তার একটি বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বিজ্ঞানীরা স্টেম সেল নিয়ে গবেষণা করবে কি করবে না, কৃত্রিমভাবে সংযুক্ত জীবন রক্ষাকারী যন্ত্র তুলে ফেলা হবে কি হবে না, স্কুলে বিবর্তনবাদ পড়ানো হবে কিনা, আর হলে কীভাবেইবা পড়াতে হবে, সবকিছুই সূক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে সরকার। বিজ্ঞানীদের গবেষণা আর কাজকর্ম নৈতিক না অনৈতিক-এ নিয়েও উপযাচক হয়ে জ্ঞানগর্ভ মত দিতে এগিয়ে আসছে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত অর্ধশিক্ষিত পাদ্রি আর যাজকেরা যুদ্ধের আগে নবী রাসুলদের মতোই ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছে সে দেশের প্রেসিডেন্ট; মিডিয়া, বৃহৎ পত্রিকা গোষ্ঠী আর প্রকাশক নির্ধারণ করে দিচ্ছে কোন খবরে আমরা বিশ্বাস করব, আর কোন খবর চেপে যাওয়া হবে। আসলে ‘মুক্ত বিশ্বের কথা মুখে বলে এভাবেই নাগরিক রুচি, চাহিদা, চেতনা আর পুরো জীবনধারাকেই নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে ধর্মান্ধ শাসককূল আর ধনকুবের গোষ্ঠী; সে অন্য এক ইতিহাস।
তবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সমস্যা হলেও আমরা মনে করি না সেটা ইসলামি সন্ত্রাসবাদের কারণ ইসলামি সন্ত্রাসবাদের উৎস মূলত ইসলামেই নিহিত। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় মহানবী মুহাম্মদ নিজে ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে বনি কু্যানুকা, ৬২৫ খ্রিস্টাব্দে বনি নাদির আর ৬২৭ খ্রিস্টাব্দে বনি কুরাইজার ইহুদি ট্রাইবকে আক্রমণ করে তাদের হত্যা করেন। বনি কুনুকার ইহুদিদের সাতশ জনকে এক সকালের মধ্যে হত্যা করতে সচেষ্ট হন (কিন্তু ‘ভণ্ড’ বলে কথিত আব্দুল্লাহ ইবনে ওবাইয়ের হস্তক্ষেপে সেটা বাস্তবায়িত হয়নি[২৬০], আর বনি কুরাইজার প্রায় আটশ থেকে নয়শ লোককে আব্দুল্লাহর বাধা উপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত হত্যা করেই ফেলেন, এমন কি তারা আত্মসমর্পণ করার পরও[২৬১]। হত্যার ভয়াবহতা এতই বেশি ছিল যে, ক্যারেন আর্মস্ট্রং-এর মতো লেখক, যিনি মুসলিম সমাজের পছন্দের তালিকায় শীর্ষস্থানীয় হিসেবে গণ্য হন, তিনি পর্যন্ত এধরনের কর্মকাণ্ডকে নাৎসি বর্বরতার সাথে তুলনা করেছেন[২৬২]। বহু বিশ্লেষকই অতীতে দেখিয়েছেন যে, বিন লাদেন, বাংলা ভাই, গোলাম আজম কিংবা মোহাম্মদ আতাসহ শীর্ষ সন্ত্রাসীরা মূলত ইসলামকে নিয়মনিষ্ঠ ভাবে অনুসরণ করেছেন। এ নিয়ে বিস্তৃতভাবে জানতে চাইলে পাঠকেরা প্রাক্তন মুসলিমদের লেখা সাম্প্রতিক বইগুলো পড়ে নিতে পারেন[২৬৩]। কিন্তু তারপরেও অনেকেই আবার আছেন যারা ইতিহাস এবং বাস্তবতা ভুলে কেবল আমেরিকাকেই সবসময় ইসলামি সন্ত্রাসবাদের উৎস বলে মনে করেন। যেমন নোয়াম চমস্কি যদিও আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে বহু বিশ্লেষণমূলক লেখা লিখেছেন এবং বাংলাদেশসহ বহু মুসলিম প্রধান দেশগুলোতে তার বিশ্লেষণ খুবই জনপ্রিয়, তিনিও মনে করেন, আমেরিকা নিজেই এক সন্ত্রাসবাদী দেশ, সে কারণেই ৯/১১-এর মতো আক্রমণ আমেরিকার ঘাড়ে এসে পড়েছে[২৬৪]। সিএনএন এর নিউজহোস্ট এবং নিউজ উইক ইন্টারন্যাশনালের এডিটর ফরিদ জাকারিয়া তার ২০০৭ সালে প্রকাশিত ‘ভবিষ্যতের স্বাধীনতা’ নামক বইয়ে বলেছেন, যদি মুসলিম সন্ত্রাসবাদের পেছনে কেবল একটি মাত্র কারণ পাওয়া যায়, তা হবে আরব বিশ্বে আমেরিকান পলিসির ব্যর্থতা[২৬৫]। নিউ এথিস্ট স্যাম হ্যারিস জবাব দিয়েছেন এই বলে, ‘হতে পারে। কিন্তু মুসলিম সন্ত্রাসবাদের উত্থান যদি সমস্যা হয়ে থাকে, তবে সমস্যার মূল কারণ হলো, ফান্ডামেন্টালস অফ ইসলাম[২৬৬]।
ধর্ম, মৌলবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ নিয়ে আলোচনার একটা বড় সমস্যা হলো অযাচিত ‘স্টেরিওটাইপিং’-এর ভয়। এধরনের আলোচনা শুরু হলেই আমরা দেখেছি বিশ্বাসীদের অনেকেই ক্ষিপ্ত হয়ে বলতে থাকেন-শুধু গুটি কয়েক সন্ত্রাসীদের কারণে সামগ্রিকভাবে ইসলামকে বা। মুসলিমদের দায়ী করা কি ঠিক হচ্ছে? একজন বিন লাদেন বা একজন মুফতি হান্নান কি ইসলামের প্রতিনিধিত্ব করে নাকি? না, সত্যিই করে না। কাজেই আমরাও বলি যে, পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম জনগোষ্ঠীকে কখনোই সন্ত্রাসী বলা উচিত নয়, যারা এধরনের ‘স্টেরিওটাইপিং করতে চান তারা ভুল করেন। এটি এক ধরনের Racism। কেউবা বলেন এটি এক ধরনের রোগ ‘ইসলামোফোবিয়া’! রোগই বলুন আর পশ্চিমা জাত্যভিমানই বলুন (যাকে প্রয়াত এডওয়ার্ড সাইদ অভিহিত করেন ‘ওরিয়েন্টালিজম’ নামে), ৯/১১-এর পর পশ্চিমা বিশ্বে বসবাসরত মুসলিমরা এধরনের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের স্বীকার হয়েছে বহু ক্ষেত্রেই-এ তো অস্বীকার করার জো নেই। মুসলিম মানেই যে ‘সন্ত্রাসী’ নয় এটি বোঝার জন্য তো কোনো দর্শন পড়ার দরকার নেই, আমার-আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই তো যথেষ্ট হওয়ার কথা। আমাদের দুজনেরই অনেক মুসলিম বন্ধু-বান্ধব রয়েছে। তাদের কেউই তো সন্ত্রাসী নন। কেউই বিন লাদেন নন, কেউই নন মুফতি হান্নান। তারা আমাদের বিপদে-আপদে খোঁজ-খবর নেন, বাসায় এসে গল্প-গুজব করেন, খাওয়া-দাওয়া করেন, এমনকি নামাজের সময় হলে এই কাফিরের বাসায় পশ্চিম দিক কোনটা জানতে চেয়ে নামাজও পড়েন। এরা নিপাট ভালো মানুষ। তারা কোরআনের কোন আয়াতে ভায়োলেন্সের কথা আছে তা সম্বন্ধে মোটেও ওয়াকিবহাল নন, সেটা নিয়ে আগ্রহীও নন-তারা আসলে স্পিরিচুয়াল ইসলামের চর্চা করেন। বিপদটা কথনোই এদের নিয়ে নয়। এরা সবাই শান্তি, ভালোবাসা আর সহিষ্ণুতায় বিশ্বাস করেন। কিন্তু এই মূল্যবোধগুলো তারা যতটা না ইসলাম থেকে পেয়েছেন, তার চেয়ে অনেক বেশি ছোটবেলা থেকেই সামাজিক শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কারণ কোনোদিন কোরআনের বা ইসলামের চর্চা না করেও তো বহু মানুষ এই গুণাবলি বর্জিত নয়, এমন প্রমাণ ভূরি ভূরি হাজির করা যায়। কিন্তু এই স্পিরিচুয়াল ইসলামের চর্চাকারী দলের বাইরেও একটা অংশ রয়েছে যারা রীতিমতো আক্ষরিকভাবে কোরআনের চর্চা করেন, চোখ-কান বন্ধ করে কোরআনের সকল আদেশ-নির্দেশ মেনে চলেন আর কোরআনের আলোকে দেশ ও পৃথিবী গড়তে চান। বিপদটা এদের নিয়েই। কারণ কেউ যদি সামাজিক শিক্ষার বদলে কোরআনের সকল আদেশ নির্দেশ চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নেন তাহলে কী হবে? সুরা আল-ইমরানের নিচের আয়াতটায় চোখ বোলানো যাক[২৬৭]–
মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোনো অমুসলিম/কাফেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না। (৩ : ২৮)।
যারা কোরআনের মধ্যে কথনও ভায়োলেন্সের চিহ্নমাত্র খুঁজে পান না, বরং পবিত্র কোরআনের আলোকে জীবন। সাজাতে চান, তারা নিজেরাই কি তাদের কোনো হিন্দু, খ্রিস্টান বা অধার্মিক প্রতিবেশীদের প্রতি কোরআনে বর্ণিত উপরের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহার করেন? তারা কি সত্যিই শুধু অমুসলিম বলেই কারো বন্ধুত্ব প্রত্যাখ্যান করেন? যদি তা না হয়, তবে বলতেই হয় যে তারা আসলে কোরআনের নির্দেশ অনুযায়ী চলছেন না। কিন্তু কোরআন তো আল্লাহর কিতাব। কেউ যদি ভাসা ভাসা উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোরআনের চর্চা না করে কোরআনের সকল নির্দেশ আক্ষরিকভাবেই মেনে চলার সিদ্ধান্ত নেন আর অবশেষে সাম্প্রদায়িক ‘তালিবান’ হিসেবে বেড়ে ওঠেন, তবে দোষটা কার হবে? সুরা আল বাকারাহ থেকে আরেকটি আয়াত দেখি-২৬৮]–
তোমাদের ওপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোনো একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা। তোমাদের জন্য কল্যাণকর (২ : ২১৬)।
অথবা সুরা আন নিসা থেকে উদ্ধৃত করা যাক[২৬৯]–
আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্ত্বা ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ের জিম্মাদার নন! আর আপনি অন্য মুসলমানদেরকেও উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ্য খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা (৪ : ৪৪)।
কোরআনের বর্ণিত নির্দেশ মতো জিহাদি জোশে উদ্বুদ্ধ হয়ে তালিবানদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইহুদি নাসারাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আফগানিস্তান চলে গিয়েছিলেন অনেকেই; কারণ ইহুদি-নাসারাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে তারা আল্লাহর নির্দেশ বলেই মেনে নিয়েছিলেন। তাদের যে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় তাও নয়। ২০০৫ সালের ১৪ই অক্টোবর দৈনিক প্রথম আলোর রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে নিষিদ্ধ ঘোষিত হরকাতুল জিহাদের তত্ত্বাবধানে আশির দশকে বাংলাদেশ থেকে প্রায় তিন হাজার মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক জিহাদি জোশে উদ্বুদ্ধ হয়ে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আফগানিস্তানে চলে গিয়েছিল। কোরআনের কিছু শিক্ষাই যে শেষ পর্যন্ত মাদ্রাসা পড়ুয়া ছাত্রদের মধ্যে ‘কাফিরদের বিরুদ্ধে অযথা হিংসা-বিদ্বেষ ছড়ানোতে বহুলাংশে দায়ী, এটি অস্বীকার করার চেষ্টা স্রেফ আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়। এ স্পর্শকাতর বিষয়টি আলোচনা করতে গেলে সবসময়ই ঘুরে ফিরে ৯/১১-এর ঘটনাটি সামনে চলে আসে। ৯/১১-এর ঘটনায় সারা পৃথিবী স্তম্ভিত হয়ে দেখেছিল কী করে কিছু ধর্মোন্মাদ জিহাদি সৈনিক উড়োজাহাজকে অস্ত্র বানিয়ে হাজার হাজার নিরপরাধ লোকের প্রাণহানি ঘটাতে পারে। যারা ইসলামের মধ্যে প্রতিনিয়ত শান্তি খোঁজেন, তারা বলবেন, এগুলো কতিপয় পথভ্রষ্ট দুষ্কৃতকারীদের কাজ-যার সাথে প্রকৃত ইসলামের কোনোই সম্পর্ক নাই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই ‘কতিপয় পথভ্রষ্ট দুষ্কৃতকারীরা তো আর নিজেদের দুষ্কৃতকারী ভাবে নি। বরং ভেবেছে তারাই সাচ্চা মুসলিম, যারা কিনা আল্লাহর দেওয়া অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছে। ৯/১১ ঘটার অনেক আগেই-১১ই জানুয়ারি ১৯৯৯-এর নিউজ উইকের একটি সংখ্যায় ওসামা বিন লাদেনের একটা সাক্ষাৎকার ছাপা হয়েছিল। সেই সাক্ষাৎকারে লাদেন পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন কেন তিনি সকল আমেরিকানদের মেরে ফেলাকে ‘জায়েজ মনে করেন। পাঠকদের উদ্দেশ্য কিছু অংশ তুলে দেওয়া হলো[২৭০]–
QUESTION : Why have you asked Muslims to target civilian Americans all over the world? Islam prohibits its followers from killing civilians in war?
BIN LADEN : If the Israelis are killing small children in Palestine and the Americans are killing the innocent people in Iraq, and if the majority of the American people support their dissolute president, this means the American people are fighting us and we have the right to target them.
QUESTION : All Americans?
BIN LADEN Muslim scholars have issued a fatwa [a religious order] against any American who pays taxes to his government. He is our target, because he is helping the American war machine against the Muslim nation.
হিন্দু ধর্মকে ইসলাম থেকে কোনো অর্থেই ভালো বলার জো নেই। যে জাতিভেদ প্রথার বিষবাষ্প প্রায় তিন হাজার বছর ধরে কুরে কুরে ভারতকে খাচ্ছে তার প্রধান রূপকার স্বয়ং ঈশ্বর। মনুসংহিতা থেকে আমরা পাই-মানুষের সমৃদ্ধি কামনায় পরমেশ্বর নিজের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহু থকে ক্ষত্রিয়, ঊরু থেকে বৈশ্য, আর পা থেকে শূদ্র সৃষ্টি করেছিলেন (১ : ৩১)। বিশ্বাসীরা জোর গলায় বলেন, ঈশ্বরের চোখে নাকি সবাই সমান! অথচ, ব্রাহ্মণদের মাথা থেকে আর শূদ্রদের পা থেকে তৈরি করার পেছনে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যটি কিন্তু বড়ই মহান! শূদ্র আর দলিত নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের প্রতি তাই ‘ঈশ্বরের মাথা থেকে সৃষ্ট উঁচু জাতের ব্রাহ্মণদের দুর্ব্যবহারের কথা সর্বজনবিদিত। সমস্ত ধনী লোকের বাসায় এখনও দাস হিসেবে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের নিয়োগ দেওয়া হয়। মনু বলেছেন-দাসত্বের কাজ নির্বাহ করার জন্যই বিধাতা শূদ্রদের সৃষ্টি করেছিলেন (৪ : ৪১৩)। এই সমস্ত নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বাসার সমস্ত কাজ সম্পন্ন করে চলে যাওয়ার পর গঙ্গা-জল ছিটিযে গৃহকে ‘পবিত্র’ করা হতো (ক্ষেত্র বিশেষে এখনও হয়)। আর হবে নাই বা কেন! তারা আবার মানুষ নাকি? তারা তো অচ্ছুৎ! শ্রী এম. সি. রাজার কথায়, ‘আপনি বাড়িতে কুকুর বিড়ালের চাষ করতে পারেন, গো-মূত্র পান করতে পারেন, এমনকি পাপ দূর করার জন্য সারা গায়ে গোবর। লেপতে পারেন, কিন্তু নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ছায়াটি পর্যন্ত আপনি মারাতে পারবেন না! এই হচ্ছে হিন্দু ধর্মের নৈতিকতা! এমনকি হিন্দু ধর্মের দৃষ্টিতে শূদ্রদের উপার্জিত ধন সম্পত্তি তাদের ভোগেরও অধিকার নেই। সব উপার্জিত ধন দাস-মালিকেরাই গ্রহণ করবে-এই ছিল মনুর বিধান-’ন হি তস্যাস্তি কিঞ্চিত স্বং ভর্তৃহার্যধনো হি সঃ (৮ : ৪১৬)। শূদ্ররা ছিল বঞ্চনার করুণতম নিদর্শন; তাদের না ছিল নাগরিক অধিকার, না ছিল ধর্মীয় বা অর্থনৈতিক অধিকার। শূদ্রদের যাতে অন্য তিন বর্ণ থেকে আলাদা করে চেনা যায় এবং শূদ্ররা যেন প্রতিটি মুহূর্তে মনে রাখে যে তিন বর্ণের মানুষের ক্রীতদাস হয়ে সেবা করার জন্যই তাদের জন্ম। তিন বর্ণের মানুষদের থেকে শূদ্ররা যে ভিন্নতর জীব তা জানানোর জন্য প্রতি মাসে মাথার সব চুল কামিযে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন মনু (৫: ১৪০)। একজন শূদ্রকে বেদ পাঠ তো দূরের কথা, শ্রবণেরও অধিকার দেওয়া হয় নি। একজন শূদ্রকে তার উঁচু জাতে বিযে করার অনুমতি পর্যন্ত দেওয়া হয় নি। একজন শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের জন্য সংরক্ষিত আসনে বসে পড়ে, তবে তার বুকে গরম লোহার রডের ছ্যাঁকা দেওয়ার অথবা পশ্চাৎদেশ কর্তন করে নেওয়ার বিধান রয়েছে (৮ : ২৪১)[২৭১]
মনুর এসব বর্ণবাদী নীতির বাস্তব রূপায়ণ আমরা দেখতে পাই রামায়ণ ও মহাভারতে। বিশেষত ধর্মশাস্ত্রীয় অনুশাসন যে শ্রেণি বৈষম্যের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতো এবং শূদ্রদের দমন-নিপীড়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো, তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ রামায়ণের শম্বুক-বধ কাহিনি। তপস্যা করার অপরাধে’ রামচন্দ্র খড়গ দিয়ে শম্বুক নামক এক শূদ্র তাপসের শিরচ্ছেদ করেন তার তথাকথিত রামরাজ্যে[২৭২]
প্রায় একই ধরনের ঘটনা আমরা দেখি মহাভারতে যখন নিষাদরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য দ্রোণাচার্যের কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখতে এলে তাকে নিচু জাতি বলে প্রত্যাখ্যান করেন দ্রোণ। শুধু তাই নয়, পরবর্তীকালে স্বশিক্ষায় শিক্ষিত একলব্যের শর নিক্ষেপের দক্ষতা নষ্ট করে ধনুর্বিদ্যায় দ্রোণের প্রিয় শিষ্য অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ণ রক্ষার অভিপ্রায়ে ‘গুরুদক্ষিণা হিসেবে একলব্যের বুড়ো আঙুল কেটে নেন তিনি। এধরনের অনেক উপকরণ ছড়িয়ে রয়েছে প্রাচীন মহাকাব্যগুলোতে[২৭৩]
আসলে এইসব প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম আদিম মানুষের সাম্যের সমাজ-কাঠামোর ভিত উপড়ে ফেলে প্রতিষ্ঠা করেছিল অসাম্য, শ্রেণিবিভক্ত সমাজের ধর্মই তৈরি করেছিল হুজুর-মজুর শ্রেণির কৃত্রিম বিভাজনের, কিংবা হয়ত বলা যায় শোষক শ্রেণিই শ্রেণিবিভক্ত সমাজের সুযোগ পুরোপুরি লাভের জন্য প্রথম থেকেই কাজে লাগিযেছিল ধর্মকে; যেভাবেই দেখি না কেন এর ফলে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সামাজিক আর অর্থনৈতিক শোষণের এই শোষণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার জন্যই ব্রাহ্মণেরা প্রচার করেছিল-ধর্মগ্রন্থগুলো স্বয়ং ঈশ্বরের মুখ-নিঃসৃত। মানুষে মানুষে বিভেদ নাকি ঈশ্বর-নির্দেশিত! ঈশ্বরকে সাক্ষী মেনে রাজনৈতিকভাবে ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত সুদূরপ্রসারী প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় উপমহাদেশের রাজনীতির গতি প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করলে।
ইসলামি জিহাদি সৈনিকদের মতোই ভারতে বিভেদের হাতিয়ার ‘সনাতন ধর্ম রক্ষায় আজ সচেষ্ট হয়েছে বিজেপি, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, বিশ্বহিন্দু পরিষদ, শিব-সেনা, বজরং দলের মতো প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলো। কয়েক দশক আগেও ভারতে নব-হিন্দুধের তেমন কোনো সংগঠিত রূপ ছিল না[২৭৪]। তবে অশিক্ষা, কুশিক্ষা আর ধর্মান্ধতার কারণে ভারতের আপামর জনসাধারণের কাছে সন্ন্যাসী, গেরুয়া, জটা, দণ্ড, রুদ্রাক্ষ, কমণ্ডলু এসব দীর্ঘকাল ধরে একটা বিমূঢ় সম্রম ভোগ করে এসেছে। ধর্মের প্রতি সাধারণ মানুষের মোহের কথা ধুরন্ধর রাজনীতিবিদরা জানে। এই ধর্মীয় ভাবালুতাকে উস্কে দিতেই বোধহয় ১৯৮৮-৯০ সালে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় দূরদর্শনে ধর্মীয় অবয়বে প্রচারিত হলো রামায়ণ আর মহাভারত। সরকারি প্রচার মাধ্যমে এভাবে অন্ধবিশ্বাসকে উৎসাহ দেওয়ার ফলে ভারতে মৌলবাদী এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দুয়ার উন্মোচিত হলো, রোপণ করা হলো এক বিষবৃক্ষের চারা। দূরদর্শনের পর্দায় প্রথমবার রামায়ণ চলাকালে কল্পিত রাম জন্মভূমি নিয়ে মৌলবাদী আন্দোলনের জোয়ার এবং পরবর্তীকালে ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলোর উত্থান সেই প্রক্রিয়ারই অংশ। জন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে তার ‘মহাকাব্য ও মৌলবাদ’ বইয়ে বলেন–
দুর্ভাগ্যবশত ভারতবর্ষে রামায়ণ ও মহাভারতকে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির মহাকাব্যিক প্রতিফলন হিসেবে অথবা ভারতীয় তথা বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য ধ্রুপদী সম্পদ হিসেবে গণ্য না করে মৌলবাদী এবং সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উপাদান হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতাই বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখানেই আমাদের গভীর লজ্জা। প্রথমে ১৯৮৮-৯০ সালে এবং আরও কয়েকবার সরকারি দূরদর্শনে রামায়ণ ও মহাভারত যে অবয়ব ও প্রকাশ-ভঙ্গিমায় সম্প্রচারিত হয়েছে, তা এই মৌলবাদী রাজনীতিতে ইন্ধন জুগিয়েছে বলেই মনে হয়। দূরদর্শনে সম্প্রচারিত রামায়ণের কাহিনি প্রধানত তুলসী দাস রচিত রামচরিত মানস গ্রন্থকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে, বাল্মীকি রামায়ণকে ভিত্তি করে নয়। তুলসী রামায়ণের কাহিনি মধ্যযুগীয় ভক্তি আন্দোলনের ফলে এবং বৈষ্ণব ভক্তি সাহিত্যের অন্তর্গত। আদি বাল্মীকি রামায়ণে বালকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ড ছিল না। আর পরবর্তীকালে সংযোজিত এই দুই কাণ্ড এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রক্ষিপ্ত কথা বাদ দিলে আদি বাল্মীকি রামায়ণে রামের অবতারত্বের বিশেষ চিহ্ন পাওয়া যায় না। মহাকাব্য হিসেবেও রামায়ণের সাহিত্যগুণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তুলসী রামায়ণে বিষ্ণুকে শ্রেষ্ঠ দেবতা রামকে বিষ্ণুর অবতার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল প্রধান লক্ষ্য। যা এমনকি বালকাণ্ড ও উত্তরকাণ্ডসহ পল্লবিত বাল্মীকি রামায়ণেরও প্রধান বিষয়বস্তু নয়। দূরদর্শনে এভাবে রামায়ণকে মহাকাব্য হিসেবে উপস্থিত না করে বিকৃতরূপে অবতারকাহিনি ও ধর্মগ্রন্থরূপেই জনসাধারণের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। সরকারি প্রচারমাধ্যমে এভাবে অন্ধবিশ্বাসকে উৎসাহ দেওয়ার ফলে মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি সঞ্জীবিত হয়েছে, এ ধারণা যুক্তিসঙ্গত। দূরদর্শনের পর্দায় প্রথমবার রামায়ণ চলাকালে রাম জন্মভূমি নিয়ে মৌলবাদী আন্দোলনের জোয়ার এবং পরবর্তীকালে তার ব্যাপক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াই এর অকাট্য প্রমাণ।
বছরখানেক আগে গুজরাটে ঘটে যাওয়া স্মরণকালের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ দাঙ্গা আমরা দেখেছি। ধর্মের মায়াজালে পড়ে সাধারণ মানুষ কী ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে আর নিষ্ঠুর আচরণ করতে পারে-গুজরাটের সাম্প্রতিক দাঙ্গা তার প্রমাণ। তারপরেও কিন্তু ধর্মের সমালোচনা করলে মৌলবাদীদের সাথে সাথে অনেক প্রগতিপন্থীরাও একাট্টা হয়ে বুক চিতিযে রুখে দাঁড়ান!
ইহুদি এবং খ্রিস্টানদের পবিত্রগ্রন্থের দিকে তাকালে দেখা যায়, পুরো বাইবেলটিতেই ঈশ্বরের নামে খুন, রাহাজানি, ধর্ষণকে বৈধতা দেওয়া হয়েছে। কিছু উদাহরণ তো দেওয়া যেতেই পারে। যুদ্ধজয়ের পর অগণিত যুদ্ধবন্দিকে কক্সা করার পর মুসা (মোশি) নির্দেশ দিয়েছিলেন ঈশ্বরের আদেশ হিসেবে সমস্ত বন্দি পুরুষকে মেরে ফেলতে[২৭৫]–
এখন তোমরা এইসব ছেলেদের এবং যারা কুমারী নয় এমন সব স্ত্রী লোকদের মেরে ফেলো; কিন্তু যারা কুমারী। তাদের তোমরা নিজেদের জন্য বাঁচিয়ে রাথো (গণনা পুস্তক, ৩১ : ১৭-১৮) I
একটি হিসেবে দেখা যায়, মুসার নির্দেশে প্রায় ১০০,০০০ জন তরুণ এবং প্রায় ৬৮,০০০ অসহায় নারীকে হত্যা করা হয়েছিল[২৭৬]। এছাড়াও নিষ্ঠুর, আক্রমণাত্মক এবং অরাজক বিভিন্ন আয়াতসমূহের বিবরণ পাওয়া যায় যিশাইয় (২১ : ৯), ১ বংশাবলী (২০ : ৩), গণনা পুস্তক (২৫ : ৩-৪), বিচারকর্তৃগণ (৮ : ৭), গণনা পুস্তক (১৬ : ৩২-৩৫), দ্বিতীয় বিবরণ (১২ : ২৯ ৩০), ২ বংশাবলী (১৪ : ৯,১৪ : ১২), দ্বিতীয় বিবরণ (১১ : ৪-৫), ১ শমুযেল (৬ : ১৯), ডটারনোমি (১৩ : ৫-৬, ১৩ : ৮-৯, ১৩ : ১৫), ১ শমুযেল (১৫ : ২-৩), ২ শমুযেল (১২ : ৩১), যিশাইয় (১৩ : ১৫-১৬), আদিপুস্তক (৯ : ৫-৬) প্রভৃতি নানা জায়গায়।
বিশ্বাসী খ্রিস্টানরা সাধারণত বাইবেলে বর্ণিত এই ধরনের নিষ্ঠুরতা এবং অরাজকতাকে প্রত্যাখ্যান করে বলার চেষ্টা করেন, এগুলো সব বাইবেলের পুরাতন নিয়মের (ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ) অধীন, যিশুখ্রিস্টের আগমনের সাথে সাথেই আগের সমস্ত অরাজকতা নির্মূল হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। এটি সত্য নয়। বাইবেলের নতুন নিয়মে যিশু খুব পরিষ্কার করেই বলেছেন যে তিনি পূর্বতন ধর্মপ্রবর্তকদের নিয়মানুযায়ীই চালিত হবেন[২৭৭]–
এ কথা মনে করো না, আমি মোশির আইন-কানুন আর নবীদের লেখা বাতিল করতে এসেছি। আমি সেগুলো বাতিল করতে আসি নি বরং পূর্ণ করতে এসেছি (মথি, ৫ : ১৭)।
খ্রিস্ট ধর্মের অনুসারীরা যেভাবে যিশুকে শান্তি এবং প্রেমের প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করে থাকেন, সত্যিকারের যিশু ঠিক কতটুকু প্রেমময় এ নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। যিশু খুব স্পষ্ট করেই বলেছেন যে–
আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি এই কথা মনে করো না। আমি শান্তি দিতে আসি নাই, এসেছি তলোয়ারের আইন প্রতিষ্ঠা করতে। আমি এসেছি মানুষের বিরুদ্ধে। মানুষকে দাঁড় করাতে; ছেলেকে বাবার বিরুদ্ধে, মেয়েকে মাযের বিরুদ্ধে, বৌকে শাশুড়ির বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে এসেছি (মথি, ১০ : ৩৪-৩৫)।
ব্যভিচার করার জন্য শুধু ব্যভিচারিণী নন, তার শিশুসন্তানদের হত্যা করতেও কার্পণ্য বোধ করেন নি যিশু[২৭৮]–
সেইজন্য আমি তাকে বিছানায় ফেলে রাখব, আর যারা তার সঙ্গে ব্যভিচার করে তারা যদি ব্যভিচার থেকে মন। না ফেরায় তবে তাদের ভীষণ কষ্টের মধ্যে ফেলব। তার ছেলেমেয়েদেরও আমি মেরে ফেলব (প্রকাশিত বাক্য, ২ : ২২-২৩)।
.
ধর্মের সমালোচনা কেন?
মানবতাবাদীরা আর যুক্তিবাদীরা কেন ধর্মগ্রন্থগুলোর সমালোচনা করেন? সমালোচনা করেন কারণ তা সমালোচনার যোগ্য, তাই। কোনোকিছুই তো আসলে সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়-তা সে অর্থনীতি বা পদার্থবিজ্ঞানের নতুন কোনো তত্বই হোক, বা মহান আল্লাহর বাণীই হোক। আসলে পুরো ধর্মবিশ্বাসই তো দাঁড়িয়ে আছে এক জলজ্যান্ত মিথ্যার ওপর ভর করে। ধর্ম মানেই আজ কিছু অবৈজ্ঞানিক চিন্তা-চেতনা, কুসংস্কার আর রীতি-নীতির সমাহার, যেগুলো কালের পরিক্রমায় উপযোগিতা হারিয়েছে। ধর্মের সমালোচনার আর একটি বড় কারণ হলো, ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে বিরাজমান নিষ্ঠুরতা। ধর্মগ্রন্থগুলো তো আর গীতাঞ্জলি বা সঞ্চিতার মতো নির্দোষ কাব্যসমগ্র নয় যে অবসর সময়ে শুয়ে শুযে কাব্য চর্চা করলাম আর তারপর আলমারির তাকে তুলে রেখে দিলাম! ধর্মগ্রন্থগুলোতে যা লেখা আছে তা ঈশ্বরের বাণী হিসেবে পালন করা হয় আর উৎসাহের সাথে সমাজে তার প্রয়োগ ঘটান হয়। হিন্দু ধর্মগ্রন্থগুলোতে বর্ণিত সতীদাহর মাহাত্ম্যকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শুধু ১৮১৫ সাল থেকে ১৮২৬ সালের মধ্যে সতীদাহের স্বীকার হয়েছে ৮১৩৫ জন নারী। এই তো সেদিনও-১৯৪৭ সালে রূপ কানোয়ার নামে একটি মেয়েকে রাজস্থানে পুড়িয়ে মারা হলো ‘সতী মাতা কী জ্য’ ধ্বনি দিয়ে। সারা গ্রামের মানুষ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল-কেউ টু শব্দটি করল না। আর করবেই বা। কেন? ধর্ম নাশ হয়ে যাবে না? মহাভারতের কথা শুনলে যেমন পুণ্য হয়, সতী পোড়ানো দেখলেও নাকি তেমনই পুণ্য লাভ হয়। ধর্ম যে কীরকম নেশায় বুঁদ করে রাখে। মানুষকে, তার জলজ্যান্ত প্রমাণ এই সতীদাহ। এজন্যই বোধহয় প্যাসকেল বলেছেন-Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction.’ খুবই সত্যি কথা চিন্তা করুন ব্যাপারটা জীবন্ত নারী-মাংস জ্বলছে, ছটফট করছে, অনেক সময় বেঁধে রাখতে কষ্ট হচ্ছে, মাঝে মাঝে পালাতে চেষ্টা করছে-আফিম জাতীয় জিনিস গিলিয়ে দিয়ে লাঠি দিয়ে খুঁচিযে আবার চিতায় তুলে দেওয়া হচ্ছে-কী চমৎকার মানবিকতা[২৭৯]! প্রায় প্রতিদিনই পত্র-পত্রিকায় পড়ছি যে, ইসলামি বিশ্বে শরিযার শিকার হয়ে প্রাণ হারাচ্ছে অসহায় সাফিয়া, আমিনারা। তবুও নেশায় ঝুঁদ হয়ে ধর্ম আর ধর্মগ্রন্থের মধ্যে শান্তি’, ‘প্রগতি’ আর ‘সহিষ্ণুতা খুঁজে চলেছেন মডারেট ধর্মবাদীরা[২৮০]।
তবে এ কথা অনস্বীকার্য যে প্রতিটি ধর্মগ্রন্থেই বেশকিছু ভালো ভালো কথা আছে (এগুলো নিয়ে আমাদের মতো নতুন দিনের নাস্তিকদের কিংবা কারোই আপত্তি করার কিছু নেই); এগুলো নিয়েই ধার্মিকেরা গর্ববোধ করেন আর এ কথাগুলোকেই নৈতিকতার চাবিকাঠি বলে মনে করেন তারা। কিন্তু একটু সংশয়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেই বোঝা যাবে ভালোবাসা প্রেম এবং সহিষ্ণুতার বিভিন্ন উদাহরণ যে ধর্মগ্রন্থ এবং তার প্রচারকদের সাথে লেবেল হিসেবে লাগিয়ে দেওয়া হয়, সেগুলো কোনোটাই ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থের জন্য মৌলিক নয়। যেমন, যিশুখ্রিস্টের অনেক আগেই লেভিটিকাস (১৯ : ১৮) বলে গেছেন, নিজেকে যেমন ভালোবাসো, তেমনই ভালোবাসবে তোমার প্রতিবেশীদের। বাইবেল এবং কোরআনে যে সহনশীলতার কথা বলা আছে, সেগুলোর অনেক আগেই (খ্রিস্টের জন্মের পাঁচশ বছর আগে) কনফুসিয়াস একই রকমভাবে বলেছিলেন ‘অন্যের প্রতি সেরকম ব্যবহার করো না, যা তুমি নিজে পেতে চাও না। আইসোক্রেটস খ্রিস্টের জন্মের ৩৭৫ বছর আগে বলে গিয়েছিলেন, ‘অন্যের যে কাজে তুমি রাগান্বিত বোধ করো, তেমন কিছু তুমি অন্যদের প্রতি করো না। এমনকি শত্রুদের ভালোবাসতে বলার কথা তাওইজমে রয়েছে, কিংবা বুদ্ধের বাণীতে, সেও কিন্তু যিশু বা মুহাম্মদের অনেক আগেই[২৮১]।
কাজেই নৈতিকতার যে উপকরণগুলোকে ধর্মানুসারীরা তাদের স্ব স্ব ধর্মের পৈত্রিক সম্পত্তি বলে ভাবছেন, সেগুলো কোনোটাই কিন্তু আসলে ধর্ম থেকে উদ্ভূত হয় নি, বরং বিকশিত হয়েছে সমাজ-বিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে। সমাজব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার স্বার্থেই সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে মানুষ কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যকে ‘নৈতিক গুণাবলি’ হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে; কারণ ওভাবে গ্রহণ না করলে সমাজব্যবস্থা অচিরেই ধ্বসে পড়তো। বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক সলোমন অ্যাশ বলেন–
আমরা এমন কোনো সমাজের কথা জানি না, যেখানে সাহসিকতাকে হেয় করা হয়, আর ভীরুতাকে সম্মানিত করা হয়; কিংবা উদারতাকে পাপ হিসেবে দেখা হয় আর অকৃতজ্ঞতাকে দেখা হয় গুণ হিসেবে।
এ ধরনের সমাজের কথা আমরা না জানার কারণ এমন সমাজ টিকে থাকতে পারে না। খুব সাদা চোখে দেখলেও, একটি সমাজে চুরি করা যে অন্যায়, এটি বোঝার জন্য কোনো স্বর্গীয় ওহি নাজিল হওয়ার দরকার পড়ে না। কারণ যে সমাজে চুরি করাকে না ঠেকিয়ে মহিমান্বিত করা হবে, সে সমাজের অস্তিত্ব লোপ পাবে অচিরেই। ঠিক একইভাবে আমরা বুঝি, সত্যি কথা বলার বদলে যদি মিথ্যা বলাকে উৎসাহিত করা হয়, তবে মানুষে মানুষে যোগাযোগ রক্ষা করাই দুরূহ হয়ে পড়বে। এ ব্যাপারগুলো উপলব্ধির জন্য কোনো ধর্মশিক্ষা লাগে না। আবার এমনও দেখা গেছে যে, শতাব্দী-প্রাচীন কোনো চলমান ব্যবস্থার পরিবর্তন মানুষ নিজে থেকেই করেছে পরিবর্তিত মূল্যবোধের কষ্টিপাথরে মানবতাকে যাচাই করে, এবং অনেকক্ষেত্রেই ধর্ম কী বলছে না বলছে তার তোয়াক্কা না করেই। দাসপ্রথার উচ্ছেদ এমনই একটি ঘটনা। বলা বাহুল্য, কোনো ধর্মগ্রন্থেই দাসত্ব উচ্ছেদের আহ্বান জানানো হয় নি। বাইবেলের নতুন কিংবা পুরাতন নিয়ম, কিংবা কোরআন, অথবা বেদ, উপনিষদ, মনুসংহিতা-কোথাওই দাসত্ব প্রথাকে নির্মল করার কথা বলা হয় নি, বরং সংরক্ষিত করার কথাই বলা হয়েছে প্রকারান্তরে। কিন্তু মানুষ সামাজিক প্রযোজনেই একটা সময় দাসত্ব উচ্ছেদ করেছে, যেমনিভাবে হিন্দু সমাজ করেছে সতীদাহ নির্মূল বা খ্রিস্ট সমাজ করেছে ডাইনি পোড়ানো বন্ধ। সতীত্ব সম্পর্কে প্রাচীন ধারণা, কিংবা সমকামিতা বা গর্ভপাতের অধিকার সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গিরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে পৃথিবী জুড়ে এ কয়েক দশকে। এ পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির অনেকগুলোই ধর্মকর্তৃক অনুমোদিত নয়।
.
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি : লেট দ্য ডেটা ডিসাইড
আজ আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর দিকে তাকালে বোঝা যায় যে, আল্লাহর গোনাহর দোহাই দিয়ে মানুষজনকে সৎ পথে পরিচালিত করার ব্যাপারটি কী নিদারুণভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। আল্লাহ বা ঈশ্বরের গোনাহর ভয় দেখিযেই যদি মানুষজনকে পাপ থেকে বিরত রাখা যেত, তা হলে রাষ্ট্রে পুলিশ-দারোগা, আইন-কানুন, কোর্ট কাচারি কোনোকিছুরই প্রয়োজন হতো না। এক ইন্টারনেট ফোরামে একটা সময় রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং ধর্মের নৈতিকতা বিষয়ে লিখতে শুরু করেছিলাম; সাথে সাথেই এক ধার্মিক ভদ্রলোক উত্তেজিত হয়ে বলতে শুরু করলেন-’অভিজিৎ রায় কিংবা রায়হান আবীরের মতো নাস্তিক লোকজন রাষ্ট্রে আছেন বলেই পুলিশ দারোগার প্রয়োজন। এধরনের উক্তিকে স্রেফ একজনমাত্র অজ্ঞ ধার্মিকের আস্ফালন বলে মনে করলে কিন্তু ভুল হবে। এধরনের ধ্যানধারণা অনেকেই মনে মনে পোষণ করেন, তাদের বেশ বড় অংশই আবার উচ্চশিক্ষিত আমেরিকার রক্ষণশীল লেখক অ্যান কোল্টার তার ‘গডলেস’ বইয়ে। মন্তব্য করেছেন, ‘সমাজ ঈশ্বরের নির্দেশিত পথে না চললে দাসত্ব, গণহত্যা, পশুবৃত্তিতে নিমজ্জিত হয়ে যাবে’[২৮২]। একই কথা উচ্চারণ করেছেন ডিসকভারি ইন্সটিউটের পুরোধা ব্যক্তিত্ব এবং ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের অন্যতম প্রবক্তা ফিলিপ জনসন একটু ভিন্নভাবে। তার মতে, যেহেতু অবিশ্বাসীরা ডারউইনের মতানুসারে মনে করে মানুষ বানর থেকে উদ্ভূত হয়েছে, সেহেতু তারা যেকোনো ধরনের ‘নাফরমানি করতে পারে-সমকামিতা, গর্ভপাত, পর্নোগ্রাফি, তালাক, গণহত্যা সবকিছু। এমন একটা ভাব, ডারউইন আসার আগ পর্যন্ত সারা পৃথিবী যেন এগুলো থেকে একেবারেই মুক্ত ছিল! ফক্স টিভির ‘ও’রাইলি ফ্যাক্টরের’ জনপ্রিয় উপস্থাপক বিল ও’রাইলি তার একটি বইয়ে লিখেছেন, ঈশ্বরের আইনের বিরুদ্ধে গেলে পুরো সমাজ নৈরাজ্য এবং অরাজকতায় পতিত হবে, আর আইন-লঙ্ঘনকারীরা সমাজকে জঙ্গল বানিয়ে ফেলবে[২৮৩]।
একজন বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি হিসেবে অ্যান কোল্টার, বিল ও’রাইলি কিংবা ফিলিপ জনসনের এধরনের আবেগপ্রবণ আপ্তবাক্যাবলীতে আমাদের বিশ্বাস করার কোনো কারণ নেই, বরং আমাদের আস্থা থাকবে বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত ফলাফলে; বিজ্ঞানীরা যেটিকে বলেন, ‘Let the data decide’। আমরা ফিলিপ জনসনের সমর্থনে এমন কোনো উপাত্ত বা ডেটা খুঁজে পাই নি যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের চাইতে বেশি অপরাধপ্রবণ; বরং কিছু পরিসংখ্যান একেবারেই উল্টো সিদ্ধান্ত হাজির করেছে। আমেরিকায় বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে নাস্তিকদের চাইতে পুনরুজ্জীবিত খ্রিস্টানদের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের হার বেশি; এও দেখা গিয়েছে, যেসব পরিবারের পরিবেশ ধর্মীযগতভাবে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল সেসমস্ত পরিবারেই বরং শিশুদের ওপর পরিবারের অন্য কোনো সদস্যদের দ্বারা বেশি যৌন নিপীড়ন হয়[২৮৪]। ১৯৩৪ সালে আব্রাহাম ফ্রান্সব্লাউ তার গবেষণাপত্রে দেখিয়েছেন ধার্মিকতা এবং সতোর মধ্যে বরং বৈরী সম্পর্কই বিদ্যমান। ১৯৫০ সালে মুর রসের গবেষণা থেকে বেরিয়ে এসেছে যে, ধার্মিকদের তুলনায় নাস্তিক এবং অজ্ঞেয়বাদীরাই বরং সমাজ এবং মানুষের প্রতি সংবেদনশীল থাকেন, তাদের উন্নয়নের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন। ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি ১৯৮৮ সালে ভারতের জেলখানায় দগী আসামীদের মধ্যে একটি জরিপ চালিয়েছিল। জরিপের যে ফল পাওয়া গিয়েছিল, তা ছিল অবাক করার মতো। দেখা গিয়েছে, আসামীদের শতকরা ১০০ জনই ঈশ্বর এবং কোনো না কোনো প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মে বিশ্বাসী[২৮৫]। আমেরিকায়ও এরকম একটি জরিপ চালানো হয়েছিল ৫ই মার্চ, ১৯৯৭ তারিখে। সে জরিপে দেখা গেছে যে আমেরিকার জনসাধারণের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ (৮-১০%) ধর্মহীন হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা কম (মাত্র ০.২১%), সে তুলনায়। ধার্মিকদের মধ্যে শতকরা হিসেবে অপরাধপ্রবণতা অনেক বেশি[২৮৬]। আমাদের ধারণা আজ বাংলাদেশে জরিপ চালালেও ভারতের মতোই ফল পাওয়া যাবে। ঈশ্বরে বিশ্বাস, পরকালে বিশ্বাস, বেহেস্তের লোভ বা দোজখের ভয় কোনোটাই কিন্তু অপরাধীদের অপরাধ থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারে নি। আল্লাহর গোনাহ কিংবা ঈশ্বরের ভয়েই যদি মানুষ পাপ থেকে, দুর্নীতি থেকে মুক্ত হতে পারত, তবে তো বাংলাদেশ এতদিনে বেহেস্তে পরিণত হতো। কিন্তু বাংলাদেশের দিকে তাকালে আমরা আজ কী দেখছি? বাংলাদেশে শতকরা ৯৯ জন লোকই আল্লা খোদা আর পরকালে বিশ্বাসী হওয়া সত্বেও দুর্নীতিতে এই দেশ মাঝেমাঝেই থাকে পৃথিবীর শীর্ষে। ধর্মে বিশ্বাস কিন্তু দেশবাসীকে দুর্নীতিমুক্ত রাখতে পারে নি। পারবেও না। যে দেশে সর্বোচ্চ পদ থেকে বইতে শুরু করে দুর্নীতির স্রোত, যে দেশে হত্যাকারী, ধর্ষক, ছিনতাইকারী, ডাকাত রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থাকার দরুন শুধু রেহাই ই পায় না, বরং বুক চিতিয়ে ঘুরে-বেড়াবার ছাড়পত্র পায়, নেতা হওয়ার সুযোগ পায়, সে দেশের মানুষ নামাজ পড়েও দুর্নীতি চালিয়ে যাবে; তারা রোজাও রাখবে, আবার ঘুষও খাবে। তাই হচ্ছে। এই তো ধর্মপ্রাণ, আল্লাহ-খোদায় বিশ্বাসী বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থা। অপরদিকে ঈশ্বরবিহীন দেশগুলোর দিকে তাকানো যাক। এই বইয়ের লেখকদ্বয়ের একজনকে (অভিজিৎ রায়) পেশাগত কারণে দীর্ঘদিন সিঙ্গাপুরে থাকতে হয়েছিল। তিনি সেখানে থাকাকালীন লক্ষ্য করেছেন যে, দেশটিতে অধিকাংশ লোকই প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মপরিচয় থেকে মুক্ত। ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অনেক চীনা ছাত্র-ছাত্রীকেই তিনি দেখেছেন ধর্মপরিচয় জিজ্ঞাসা করলে তারা বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলে-’ফ্রি থিঙ্কার। অথচ ধর্ম নয়, শুধু আইনের শাসন আর সামাজিক মূল্যবোধগুলোর চর্চা করে সিঙ্গাপুর আজ পৃথিবীর সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর একটি। অধিকাংশ সিঙ্গাপুরবাসীরা আল্লাহ-খোদার নামও করেন না, নরকের ভয় অথবা বেহেস্তের লোভও তাদের নেই। কোন জাদুবলে তারা তাহলে দুর্নীতি থেকে মুক্ত থাকছে?
এটি লেখকের ব্যক্তিগত উপলব্ধি ভাবলে ভুল হবে। সাম্প্রতিককালে বহু আন্তর্জাতিক গবেষকই এই পর্যবেক্ষণের সাথে একমত পোষণ করেন। যেমন, গবেষক ফিল জুকারম্যান ২০০৫ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে সমীক্ষা চালিয়েছেন। সেসব দেশগুলোতে ঈশ্বরে বিশ্বাস এখন একেবারেই নগণ্য। যেমন, সুইডেনে জনসংখ্যার প্রায় ৮৫ ভাগ এবং ডেনমার্কে প্রায় ৪০ ভাগ লোক এখন ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না[২৮৭]। অথচ সেসমস্ত ‘ঈশ্বরে অনাস্থা পোষণকারী দেশগুলোই আজ পৃথিবীতে সবচেয়ে কম দুর্নীতিগ্রস্থ এবং সবচেয়ে কম সহিংস দেশ হিসেবে চিহ্নিত। ফিল জুকারম্যান তার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সম্প্রতি একটি বই লিখেছেন, ‘ঈশ্বরবিহীন সমাজ’ শিরোনামে[২৮৮]। তিনি সেই বইয়ে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন যে, ডেনমার্কের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর আরহাসে থাকা সময়গুলোতে কোনো পুলিশের গাড়ি দেখেন নি বললেই চলে। প্রায় ৩১ দিন পার করে তিনি প্রথম একটি পুলিশের গাড়ি দেখেন রাস্তায়। পুরো ২০০৪ সালে মাত্র একজন লোক হত্যার খবর প্রকাশিত হয়। এ থেকে বোঝা যায় এ সমস্ত দেশগুলোতে মারামারি হানাহানি কত কম। শুধু তাই নয়, সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে ডেনমার্ক পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী দেশ[২৮৯]
উপরের পরিসংখ্যানগুলো দেওয়ার উদ্দেশ্য এটা প্রমাণ করা নয় যে, মানুষ নাস্তিক হলেই ভালো হবে কিংবা আস্তিক হলেই খারাপ হবে, বরং এটাই বোঝানো যে, ধর্ম কোনোভাবেই নৈতিকতার ‘মনোপলি ব্যবসা’ দাবি করতে পারে না। আসলে কোনো বিশেষ ধর্মের আনুগত্যের ওপর কিন্তু মানুষের নৈতিক চরিত্র-গঠন নির্ভর করে না, নির্ভর করে একটি দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট আর সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিবেশের ওপর। আসলে আধুনিক যুগের জীবনযাত্রার প্রেক্ষাপটে এ কথা বলা যায়, প্রাচীনকালের ধর্মগ্রন্থগুলোর আলোকে নৈতিকতাকে বিশ্লেষণ করলে আর চলবে না, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনুসন্ধান এবং বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে।
প্রখ্যাত মনোবিদ, বিজ্ঞানের দার্শনিক এবং স্কেপটিক ম্যাগাজিনের প্রতিষ্ঠাতা ড. মাইকেল শারমার মানবসমাজে মূল্যবোধ এবং নৈতিকতার অভিব্যক্তি নিয়ে আলাদা করে ভেবেছেন এবং এ নিয়ে লিখেছেন। তিনি তার ‘দ্য সায়েন্স অফ গুড অ্যান্ড এভিল’ গ্রন্থে ব্যাখ্যা। করেছেন সমাজ বিকাশের প্রযোজনেই মানুষ কিছু নীতিকে প্রথম থেকে ‘গোল্ডেন রুল’ হিসেবে গ্রহণ করেছিল[২৯০]–
Do unto others, as you would have them do unto you. (অন্যদের প্রতি সেরকম ব্যবহারই করো যা তুমি তাদের থেকে পেতে চাও)।
কারণ এই নীতির অনুশীলন ছাড়া কোনো সমাজব্যবস্থা টিকে থাকবে না। মাইকেল শারমার তার গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, মানব বিবর্তনের ধারাতেই পারস্পরিক প্রতিযোগিতার পাশাপাশি আবার নৈতিকতা, মূল্যবোধ, সহনশীলতা, উদারতা, স্বার্থত্যাগ, সহানুভূতি, সমবেদনা প্রভৃতি গুণাবলির চর্চা হয়েছে। সভ্যতার প্রতিনিয়ত সংঘাত ও সংঘর্ষেই গড়ে উঠেছে মানবীয় ‘গ্রেভিশনাল এথিকস’, যা মানুষকে প্রকৃতিতে টিকে থাকতে সহায়তা করেছে।
.
বিবর্তন ও নৈতিকতার উদ্ভব
একটা সময়ে ধর্মবাদীরা একচেটিয়াভাবে নৈতিকতার উৎসের জন্য ধর্ম এবং ঈশ্বরকে সাক্ষীগোপাল হিসেবে উপস্থাপন করতেন। তারা বহুকাল ধরেই নৈতিকতার পুরো ব্যাপারটাকে ঐশ্বরিক প্রলেপ লাগিয়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন এবং দাবি করেছেন (এবং এখনও অনেকে করেন) যে, জৈববৈজ্ঞানিকভাবে নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের উদ্ভবের মতো ব্যাপারগুলো ব্যাখ্যা করা যাবে না। এগুলোর কোনো জৈবিক ব্যাখ্যা নেই। এগুলোর ব্যাখ্যা একমাত্র ঈশ্বর। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা বৈজ্ঞানিক মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হয় নি মোটেই, বরং বিজ্ঞানীরা বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কীভাবে পরার্থতা কিংবা সহযোগিতার মতো ব্যাপারগুলো প্রাণিজগতে উদ্ভূত হয়েছে তার বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হয়েছেন। এমনকি ডারউইন নিজেও তার সময়ে জেনেটিক্সের কোনো জ্ঞান ছাড়াই কেবল জীবজগৎ পর্যবেক্ষণ করে সহযোগিতা এবং পরার্থতার বিবর্তনীয় উপযোগিতা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানী, দার্শনিক এবং চিন্তাবিদেরা বহুভাবে দেখিয়েছেন যে এই ডারউইনীয় পদ্ধতিতে প্রাকৃতিকভাবেই পরার্থপরায়ণতা, সহযোগিতা, নৈতিকতা আর মূল্যবোধের মতো অভিব্যক্তিগুলো জীবজগতে উদ্ভূত হতে পারে, যা বিবর্তনের পথ ধরে মানবসমাজে এসে আরও বিবর্ধিত আর বিকশিত হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়গুলোতে জীববিজ্ঞান, সাংস্কৃতিক এবং বিবর্তনীয় উৎসের সন্ধান করে বহু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ এবং গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে[২৯১]।
একটু খেয়াল করলেই দেখা যাবে যে, নৈতিকতার ব্যাপারটি যে শুধু মানবসমাজেরই একচেটিয়া তা নয়, ছোট স্কেলে তথাকথিত অনেক ‘ইতর প্রাণী জগতের মধ্যেও কিন্তু এটি দেখা যায়। ভ্যাম্পায়ার বাদুড়েরা নিজেদের মধ্যে খাদ্য ভাগাভাগি করে, বানর এবং গরিলারা তাদের দলের কোনো সদস্য মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকলে তাকে সহায়তা করার জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা করে, এমনকি ‘দশে মিলে কাজ করে তার জন্য খাবার পর্যন্ত নিয়ে আসে। ডলফিনেরা অসুস্থ অপর সহযাত্রীকে ধাক্কা দিয়ে সৈকতের দিকে নিয়ে যায়, যার ফলে অসুস্থ ডলফিনটির পর্যাপ্ত আলো বাতাস পেতে সুবিধা হয়, তিমি তাদের দলের অপর কোনো আহত তিমিকে দ্রুত সারিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। হাতিরা তাদের পরিবারের অসুস্থ বা আহত সদস্যকে বাঁচানোর জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে। এধরনের দৃষ্টান্ত বিরল নয়।
বিবর্তন তত্ব আমাদের খুব ভালোভাবেই দেখিয়েছে জিনগত স্তরে স্বার্থপরতা কিংবা প্রতিযোগিতা কাজ করলেও, জিনের এই স্বার্থপরতা থেকেই পরার্থতার মতো অভিব্যক্তির উদ্ভব ঘটতে পারে। এ ব্যাপারটি শিক্ষায়তনে গবেষণার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো তুলে ধরেন বিজ্ঞানী উইলিয়াম হ্যামিলটন। পরবর্তীকালে ধারণাটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন স্বনামখ্যাত বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স তার ‘সেলফিশ জিন’ বইয়ের মাধ্যমে[২৯২]। এই বইয়ের মাধ্যমেই আসলে জীববিজ্ঞানীরা সমাজ এবং জীবনকে ভিন্নভাবে দেখা শুরু করলেন। পরার্থতা, আত্মত্যাগ, দলগত নির্বাচনের মতো যে বিষয়গুলো আগে বিজ্ঞানীরা পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করতে পারতেন না, সেগুলো আরও বলিষ্ঠভাবে জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করতে পারলেন। শুধু মানুষ নয় অন্য যেকোনো প্রাণীর মধ্যেই সন্তানদের প্রতি অপত্য স্নেহ প্রদর্শন কিংবা সন্তানদের রক্ষা করার জন্য মা-বাবারা সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে। অর্থাৎ, নিজের দেহকে বিনষ্ট করে হলেও পরবর্তী জিনকে রক্ষা করে চলে। পরবর্তী জিন’ রষ্কা না পেলে নিজের দেহ যত সুষম, সুন্দর, শক্তিশালী আর মনোহর কিংবা নাদুস-নুদুস হোক না কেন, বিবর্তনের দিক থেকে কোনো অভিযোজিত মূল্য নেই। সেজন্যই নেকড়ে যখন আক্রমণ করে, গোত্রের ছোট বাচ্চাদের রক্ষা করার জন্য বুনো মোষেরা বাচ্চাদের চারিদিকে ঘিরে শিং উঁচিযে নেকডের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে, নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করে হলেও। এভাবেই জীব বিবর্তনের পথ ধরে তার জিন-বিস্তারে কিংবা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রক্ষায় উদ্যোগী হয় টিকে থাকার প্রযোজনেই। আসলে যার সাথে সে বেশি জিন বিনিময় করবে, যত ঘনিষ্ঠতা বাড়াবে, তত বাড়বে নিজের জিন বিস্তারের সম্ভাবনা সেজন্যই সন্তানের প্রতি, পরিবারের প্রতি, নিকটাত্মীযের প্রতি এবং গোত্রের প্রতি এক ধরনের জৈবিক টান উপলব্ধি করে এবং তাদেরকে রক্ষার চেষ্টা করে। বিজ্ঞানীরা আরও দেখেছেন, স্বার্থপর জিন যেমন আত্মত্যাগ কিংবা পরার্থতা তৈরি করে, ঠিক তেমনই আবার প্রতিযোগিতামূলক জীবন সংগ্রাম থেকেই জীবজগতে তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের পারস্পরিক সহযোগিতা, মিথোজীবিতা কিংবা সহ বিবর্তন। টিকে থাকার প্রয়োজনেই কিন্তু এগুলো ঘটে। শিকারি মাছদের থেকে বাঁচার জন্য ক্লাউন মাছদের সাথে এনিমোনের সহবিবর্তন, হামিং বার্ডের সাথে অর্নিয়োপথিলাস ফুলের সহবিবর্তন, এংরাকোমিড অর্কিডের সাথে আফ্রিকান মথের সহবিবর্তন এগুলোর প্রত্যক্ষ উদাহরণ প্রকৃতিতেই আছে।
কোনো শিকারি পাখি যখন কোনো ছোট পাখিকে লক্ষ্য করে আক্রমণ করে, তখন অনেক সময় দেখা যায় যে, গোত্রের অন্য পাখি চিৎকার করে ডেকে উঠে তাকে সতর্ক করে দেয়। এর ফলে সেই শিকারি পাখি আর তার আদি লক্ষ্যকে তাড়া না করে ওই চিৎকার করা পাখিটিকে আক্রমণ শুরু করে। এই ধরনের পরার্থতা এবং আত্মত্যাগ কিন্তু প্রকৃতিতে খুব স্বাভাবিকভাবেই দেখা যায়। এই ব্যাপারগুলো বিবর্তনের কারণেই উদ্ভূত হয়েছে। মুক্তমনায় সম্প্রতি বিবর্তন ও নৈতিকতার উদ্ভব’ শিরোনামে দুই পর্বের একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে[২৯৩]। সেই প্রবন্ধটিতে বাংলায় প্রথমবারের মতো মেনার্ড স্মিথসহ অন্যান্য বিজ্ঞানীদের গাণিতিক মডেলের উল্লেখ করে দেখানো হয়েছে যে, শুধু প্রতিযোগিতা কিংবা বিবাদ করলে জিনপুলকে সর্বোচ্চ দক্ষতায় বাঁচিয়ে রাখা যায় না, সাথে আনতে হয় সহযোগিতা এবং পরার্থতার কৌশলও। কাজেই ঈশ্বর কিংবা কোনো বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাস নয়, এই মুহূর্তে নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের উদ্ভবকে সফলভাবে ব্যাখ্যা করতে পারছে বিবর্তন তত্ব।
ছবি। পেজ ৩৪৭
চিত্র : ক্লাউন মাছ আর এনিমোনের সহবিবর্তন-প্রকৃতিতে এরকম সহযোগিতার উদাহরণ আছে বহু।
.
নৈতিকতার জন্য ধর্মের কি আর কোনো প্রয়োজন আছে?
একটা সময় হয়ত ধর্মীয় নৈতিক বিধানগুলোর একটা ইতিবাচক ভূমিকা ছিল সমাজের ওপর। নানা ধরনের ধর্মীয় বিধানই ছিল আইন, ওগুলোই ছিল সুনীতিবোধ গড়ে তোলার ভিত্তিভূমি। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগামীতার সাথে সাথে ধর্মীয় প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাচ্ছে, অনেক আগেই ফুরিযেছে ধর্মপ্রবর্তকদের ভূমিকাও। আজ আধুনিক মননের অধিকারী মানুষের কাছে প্রাচীন উপাসনা ধর্মগুলো একেবারেই অপায়ে হয়ে উঠেছে। কেউই আজ বিশ্বাস করে না তন্ত্রমন্ত্রে অসুখ সারে, কিংবা ‘আল্লাহ মেঘ দে পানি দে বলে ডাকলেই বৃষ্টি ঝরে। সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখতেও আজ ধর্মগুরু, নবী কিংবা পয়গম্বরদের ‘মহান মিথ্যার চেয়ে ধর্মনিরপেক্ষ বিজ্ঞানমনস্ক সমাজ, আইনের শাসন আর সাংস্কৃতিক অগ্রগতি অনেক বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। ধর্মকেন্দ্রিক নৈতিকতার বিষয়গুলো অগ্রণী চিন্তার মানুষদের কাছে। গুরুত্বহীন, তাদের মতো ধর্মমুক্ত মানুষেরাই হয়ত আগামীর পরিবর্তিত বিশ্বে নির্ধারণ করবে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের এক নতুন সংজ্ঞা।
০৮. বিশ্বাসের ভাইরাস
অনিষ্টকর কর্ম মানুষ কখনোই অতোটা অন্তপ্রাণভাবে ও সানন্দে করে না, যতোটা সে করে ধর্মীয় বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে করার সময়। –প্যাসকেল
সাম্প্রতিক সময়গুলোতে বিশ্বজুড়েই আত্মঘাতী বোমা হামলা এবং ‘সুইসাইড টেরোরিজম’-এর মাধ্যমে নির্বিচারে হত্যা এবং আতঙ্ক তৈরি ধর্মীয় উগ্রপন্থী দলগুলোর জন্য খুব জনপ্রিয় একটা পদ্ধতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর আল কায়দার উনিশ জন সন্ত্রাসী চারটি যাত্রীবাহী বিমান দখল করে নেয়। তারপর বিমানগুলো কক্সা করে আমেরিকার বৃহৎ দুটি স্থাপনার ওপর ভয়াবহ হামলা চালায় তারা। নিউ ইয়র্কের বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্র বা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের টুইন টাওয়ার এবং ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর (পেন্টাগন)– এ ওই হামলা চালানো হয়। প্রায় তিন হাজার মানুষ সেই হামলায় মৃত্যুবরণ করে। আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসবাদী হামলা ছিল এটি। এই হামলার পেছনে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণ থাকলেও এটি অনস্বীকার্য যে এর পেছনে সবচেয়ে বড় মদদ আসলে বিশ্বাস নির্ভর ধর্মীয় উগ্রতা।
একটা প্রশ্ন আমাদের বরাবরই উদ্বিগ্ন করে। কেন এইসব তরুণ সন্ত্রাসবাদের পথ বেছে নিচ্ছে? কেন তারা হয়ে উঠছে আত্মঘাতী? কেন তারা ঘটনা তো একটা দুটো নয়, বিশ্বজুড়েই ঘটে চলেছে শত শত। বাংলাদেশেই কি আমরা কিছুদিন আগে বাংলা ভাইযের তাণ্ডব দেখি নি? ইসলামের নামে দেশের প্রতিটি জেলায় বোমাবাজি, কিংবা রমনা বটমূলে কিংবা সিনেমা হলগুলোর মতো ‘বে-শরিয়তী জায়গাগুলোর ওপর আগ্রাসন, চট্টগ্রাম আদালতে আত্মঘাতী বোমার তাণ্ডবে জগন্নাথ পাঁড়ের মৃত্যু, পত্রিকার পাতায় ঘাতকাহত হুমায়ুন আজাদ কিংবা ব্লগার থাবা বাবার রক্তাক্ত ছবি? ২০১২ সালের অক্টোবর মাসে কাজী মোহাম্মদ রেজওয়ানুল আহসান নাফিস নামের একুশ বছরের এক বাংলাদেশী যুবক যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে গ্রেফতার হয়ে বিশ্বব্যাপী পত্র-পত্রিকার আলোচিত খবর হয়েছিলেন[২৯৪] এগুলোর ভিত্তি কী? ২০০৫ সালের পর শুধু মুম্বাইযেই সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটেছে অন্তত দশটি, যেগুলোর সাথে ইসলামি সন্ত্রাসবাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে বলে মনে করা হয়। এর আগে রামজন্মভূমিকে ইস্যু করে উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের সন্ত্রাস, বাবরি মসজিদ ধ্বংস কিংবা গুজরাটে দাঙ্গাও দেখেছি আমরা। এগুলোরই বা কারণ কী? এধরনের ঘটনা। ঘটলেই খুব জোরেশোরে একটি কারণকে সামনে নিয়ে আসা হয়: বিদ্যমান সামাজিক অনাচার। ২০০১ সালে সেপ্টেম্বর ১১-এর রক্তাক্ত ঘটনার পর পরই নোয়াম চমস্কি বলেছিলেন, ‘আমেরিকা নিজেই এক সন্ত্রাসী রাষ্ট্র, যার কর্মকাণ্ডই নাইন-ইলেভেনকে নিজের ওপর টেনে এনেছে[২৯৫]। তবে সব বিশ্লেষকই যে চমস্কির ঢালাও মন্তব্যের সাথে একমত হয়েছেন তা নয়। যেমন, শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ব্রুস লিঙ্কন তার Holy Terrors, Thinking About Religion After September 11’ গ্রন্থে পরিষ্কার করেই বলেছেন[২৯৬]–
ধর্মের কারণেই আতা এবং তাদের অন্যান্য সহযোগীরা মনে করেছে এধরনের আক্রমণ শুধু নৈতিক নয়, সেইসাথে পবিত্র দায়িত্ব।
আতা নিজেও তার সুটকেসে কোরআন বহন করছিলেন। ধ্বংসাবশেষ থেকে উদ্ধারকৃত আতার কাছ থেকে পাওয়া তার শেষ নির্দেশাবলীগুলোও সেই সাক্ষ্যই দেয় যে, তারা পবিত্র আল্লাহ এবং ইসলামের প্রেরণাতেই এই জিহাদে অংশ নিয়েছিলেন। সেই নির্দেশাবলীতে আতা খুব গুরুত্ব দিয়েই বলেছিলেন-কীভাবে আল্লাহর নামে যাত্রা শুরু করতে হবে, কীভাবে অস্ত্র তৈরি রাখতে হবে, কীভাবে নিজের দেহকে কোরআনের আয়াত দিয়ে আশীর্বাদধন্য করে নিতে হবে, কীভাবে ঘটনা ঘটানোর সময় সুরা পাঠ করে যেতে হবে, ইত্যাদি[২৯৭]।
‘পবিত্র ধর্মগ্রন্থগুলোর প্রভাব সাধারণ মানুষদের কাছে ব্যাপক, এমনকি এই আধুনিক সমাজেও। সেজন্যই প্রাচীন ধর্মগ্রন্থগুলোর অমানবিক আয়াত কিংবা শ্লোকগুলো সন্ত্রাস এবং সহিংসতাকে উস্কে দিতে পারে। সহিংসতার সাথে যে ধর্মের বাণীর অনেক সময়ই সরাসরি সম্পৃক্ততা থাকে তার ব্যাখ্যা জ্যাক নেলসন প্যালম্যের দিয়েছেন তার ইজ রিলিজিয়ন কিলিং আস?” গ্রন্থে [২৯৮]। তিনি বলেন–
Violence is widely embraced because it is embedded and sanctified in sacred texts and because its use seems logical in a violent world.
একই ধরনের কথা বলেছেন নতুন দিনের নাস্তিক স্যাম হ্যারিস তার নিউইয়র্ক টাইমস বেস্ট সেলার এন্ড অফ ফেইথ’ গ্রন্থে[২৯৯] তিনি তার বইয়ে দেখিয়েছেন অতিমাত্রায় মধ্যযুগীয় বিশ্বাস নির্ভরতার কারণেই সন্ত্রাস আর জিহাদ এখনও করাল গ্রাসের মতো থাবা বসিয়ে আছে আমাদের সমাজে। তিনি মনে করেন আধুনিক সভ্যতার জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিরিখে মধ্যযুগীয় বিশ্বাস নির্ভর ব্যবস্থা আজ অচল। এগুলো পরিত্যাগের সময় এসেছে আজ।
কিন্তু তারপরেও সামাজিক অনাচারের ব্যাপারটা থাকবেই। অনেক সময় সামাজিক অনাচার, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক শোষণ, নির্যাতন এবং নিপীড়ন মিলেমিশে এমনই একাকার হয়ে যায় যে আলাদা করা মুশকিলই হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক যেমন হয়েছিল, ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর ভারতের মুম্বাইযে। সেইদিন প্রায় ১০জন জঙ্গি সবমিলিয়ে তাজ হোটেলসহ মুম্বাইযের ৫টা বিখ্যাত ল্যান্ডমার্ক আক্রমণ করে, গোলাগুলি করে নিমেষের মধ্যে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। হামলায় দেড়শ জনেরও বেশি লোক মারা গিয়েছিল। ঘটনার পরপরই ডেকান মুজাহিদিন নামের একটি অজানা সন্ত্রাসী গ্রুপ ঘটনার দায়দায়িত্ব স্বীকার করে। কিন্তু পরবর্তীকালে পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদী গ্রুপ লস্কর-ই-তৈয়বার সংশ্লিষ্টতা প্রমাণিত হয়[৩০০]। এছাড়াও আলকায়দা, জয়সে মুহাম্মদ, ভারতীয় মুজাহিদিন এবং সর্বোপরি অন্যান্য পাকিস্তানি টেরর গ্রুপের জড়িত থাকার সম্ভাবনাও অনুমিত হয়েছে মিডিয়ায়। নিহত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পাঁচজন আমেরিকানসহ পনেরো জন বিদেশির মৃত্যুর ব্যাপারটা নিশ্চিত করা হয়েছিল। সিএনএন পুরো দুই-তিন দিন ধরে ভারতের ঘটনাবলী সরাসরি সম্প্রচার করেছিল। ঘটনার ভয়াবহতা এতই বেশি ছিল যে, অনেকেই ঘটনাটিকে ভারতের ৯/১১ হিসেবে চিহ্নিত করে ফেলেছিলেন। নাইন ইলেভেনের ঘটনার সময় যেমনটি হয়েছিল, ঠিক তেমনই এসময়েও বহু বিশেষজ্ঞ এর পেছনে কাশ্মীর সমস্যা, সামাজিক অনাচার, মুসলিমদের প্রতি ভারতের বৈমাত্রেয় মনোভাবসহ বহু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সন্ধানে তৎপর হলেও এর পেছনে বড় একটা কারণ যে ধর্মীয় ছিল তা সন্দেহাতীত। মূলত হোটেল তাজের সেই সন্ত্রাসবাদী হামলার পরিপ্রেক্ষিতেই এই ‘বিশ্বাসের ভাইরাস’ নামের লেখাটির সূত্রপাত ঘটেছিল এবং এটি মুক্তমনা এবং সচলায়তন ব্লগে প্রকাশের পর বহু পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, উন্মোচন করেছিল পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনার দুয়ার[৩০১]। বইয়ের এই অধ্যায়টি সেই প্রবন্ধেরই আনুষঙ্গিক বিস্তৃতি।
বিশ্বাস নির্ভর সন্ত্রাসবাদ এত ব্যাপক আকারে মহামারি রূপে ছড়িয়ে পড়ার পেছনে কোনো নৃতাত্ত্বিক, মনস্তাত্বিক কিংবা জৈববৈজ্ঞানিক কারণ আছে কিনা তা খুঁজে দেখাকে আমরা আসলেই এখন জরুরি মনে করি। বিবর্তনবাদ কি এ ব্যাপারে আমাদের কোনো পথ দেখাতে পারে? অনেক সামাজিক জীববিজ্ঞানীই কিন্তু মনে করেন পারে। আমরা আগের অধ্যায়ে বিবর্তনের মাধ্যমে নৈতিকতার উদ্ভব নিয়ে সামান্য আলোচনা করেছিলাম। এই অধ্যায়ে আমরা সেই একই প্রক্রিয়ায় করব বিশ্বাস নির্ভরতার অনুসন্ধান।
আমরা যতই নিজেদের যুক্তিবাদী কিংবা অবিশ্বাসী বলে দাবি করি না কেন, এটা তো অস্বীকার করার জো নেই-’বিশ্বাসের একটা প্রভাব সবসময়ই সমাজে বিদ্যমান ছিল। না হলে এই বিংশ শতাব্দীতে এসেও প্রাচীন ধর্মগুলো স্রেফ মানুষের বিশ্বাসকে পুঁজি করে এভাবে টিকে থাকে কীভাবে? এখানেই হয়ত সামাজিক বিবর্তনবাদের তত্বগুলো গুরুত্বপূর্ণ। এটা মনে করা ভুল হবে না যে, বিশ্বাস’ ব্যাপারটা মানবজাতির বেঁচে থাকার পেছনে হয়ত কোনো বাড়তি উপাদান যোগ করেছিল একটা সময়। মানুষ আদিমকাল থেকে বহু সংঘাত, মারামারি এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে গিয়ে আজ এই পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। একটা সময় সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করাটা ছিল মানবজাতির টিকে থাকার ক্ষেত্রে অনেক বড় নিয়ামক। যে গোত্রে বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিতে পারা গিয়েছিল যে যোদ্ধারা সাহসের সাথে যুদ্ধ করে মারা গেলে পরলোকে গিযে পাবে অফুরন্ত সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, হুর পরী উদ্ভিন্নযৌবনা চিরকুমারী অপ্সরা, (আর বেঁচে থাকলে তো আছেই সাহসী যোদ্ধার বিশাল সম্মান আর পুরস্কার)–তারা হয়ত অনেক সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ। করেছে এবং নিজেদের এই যুদ্ধংদেহী জিন’ পরবর্তী প্রজন্মে বিস্তৃত করতে সহায়তা করেছে। আমাদের মুক্তমনা সাইটে রিচার্ড ডকিন্সের একটি চমৎকার প্রবন্ধ রাখা আছে ধর্মের উপযোগিতা নামে প্রবন্ধটিতে অধ্যাপক ডকিন্স একজন বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানীর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্বাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন[৩০২]।
ডকিন্সের লেখাটি থেকে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করা যাক। মানব সভ্যতাকে অনেকে শিশুদের মানসজগতের সাথে তুলনা করেন। শিশুদের বেঁচে থাকার প্রযোজনেই একটা সময় পর্যন্ত অভিভাবকদের সমস্ত কথা নির্দ্বিধায় মেনে চলতে হয়-এ আমরা জানি। ধরা যাক একটা শিশু চুলায় হাত দিতে গেল, ওমনি তার মা বলে উঠল- ‘চুলায় হাত দেয় না, ওটা গরম!, ওটা গরম! শিশুটা সেটা শুনে আর হাত দিল না, বরং সাথে সাথে হাত সরিয়ে নিল। মার কথা শুনতে হবে-এই বিশ্বাস পরম্পরায় আমরা বহন করি-নইলে যে আমরা টিকে থাকতে পারব না, পারতাম না। এখন কথা হচ্ছে-সেই। ভালো মা-ই যখন অসংখ্য ভালো উপদেশের পাশাপাশি আবার কিছু মন্দ বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন উপদেশও দেয় ‘শনিবার ছাগল বলি না দিলে অমঙ্গল হবে’; কিংবা ‘রসগোল্লা থেযে অংক পরীক্ষা দিতে যেও না। গেলে গোল্লা পাবে’ জাতীয়-তখন শিশুর পক্ষে সম্ভব হয় না সেই মন্দ বিশ্বাসকে অন্য দশটা বিশ্বাস কিংবা ভালো উপদেশ থেকে আলাদা করার। সেই মন্দ বিশ্বাসও বংশপরম্পরায় সে বহন করতে থাকে অবলীলায়। সব বিশ্বাস খারাপ নয়, কিন্তু অসংখ্য মন্দ বিশ্বাস হয়ত অনেক সময় জন্ম দেয় বিশ্বাসের ভাইরাসের’। এগুলো একটা সময় প্রগতিকে থামাতে চায়, সভ্যতাকে ধ্বংস করে। উদাহরণ হিসেবে, ডাইনি পোড়ানো, সতীদাহ, বিধর্মী এবং কাফেরদের প্রতি ঘৃণা, মুরতাদ হত্যার কথা বলা যায়।
.
বিশ্বাসের ভাইরাস
‘বিশ্বাসের ভাইরাস ব্যাপারটা এই সুযোগে আর একটু পরিষ্কার করে নেওয়া যাক। একটা মজার উদাহরণ দেই ড্যানিয়েল ডেনেটের সাম্প্রতিক ‘ব্রেকিং দ্য স্পেল বইটি থেকে[৩০৩]। আপনি নিশ্চয়ই ঘাসের ঝোপে কিংবা পাথরের উপরে কোনো পিঁপড়াকে দেখেছেন-সারাদিন ঘাসের নিচ থেকে ঘাসের গা বেয়ে কিংবা পাথরের গা বেয়ে উপরে উঠে যায়, তারপর আবার ঝপ করে পড়ে যায় নিচে, তারপর আবারও গা বেয়ে উপরে উঠতে থাকে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে-এই বেআক্কেল কলুর বলদের মতো পশুশ্রম করে পিপড়াটি কী এমন বাড়তি উপযোগিতা পাচ্ছে যে,এই অভ্যাসটা টিকে আছে? কোনো বাড়তি উপযোগিতা না পেলে সারাদিন সে এই অর্থহীন কাজ করে সময় এবং শক্তি ব্যয় করার তো কোনো মানে হয় না। আসলে সত্যি বলতে কী, এই কাজের মাধ্যমে পিঁপড়াটি বাড়তি কোনো উপযোগিতা তো পাচ্ছেই না, বরং ব্যাপারটি সম্পূর্ণ উল্টো। গবেষণায় দেখা গেছে পিঁপড়ার মগজে থাকা ল্যাংসেট ক্লক নামে এক ধরনের প্যারাসাইট এর জন্য দায়ী। এই প্যারাসাইট বংশবৃদ্ধি করতে পারে শুধু তখনই যখন কোনো গরু বা ছাগল একে ঘাসের সাথে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে। ফলে প্যারাসাইটটা নিরাপদে সেই গরুর পেটে গিযে বংশবৃদ্ধি করতে পারে। পুরো ব্যাপারটাই এখন জলের মতো পরিষ্কার-যাতে পিপড়াটা কোনোভাবে গরুর পেটে ঢুকতে পারে সেই দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ঘাস বেয়ে তার ওঠানামা। আসলে ঘাস বেয়ে ওঠানামা পিঁপড়ার জন্য কোনো উপকার করছে না বরং ল্যাংসেট ফুক কাজ করছে এক ধরনের ভাইরাস হিসেবে-যার ফলে পিঁপড়া বুঝে বা না বুঝে, তার দ্বারা চালিত হচ্ছে।
ছবি। পেজ ৩৫৭
চিত্র : ল্যাংসেট ফুক নামের প্যারাসাইটের কারণে পিঁপড়ার মস্তিষ্ক আক্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন পিঁপড়া কেবল চোখ বন্ধ করে পাথরের গা বেয়ে ওঠানামা করে। ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোও কি মানুষের জন্য একেকটি প্যারাসাইট?
এধরনের আরও কিছু উদাহরণ জীববিজ্ঞান থেকে হাজির করা যায়। নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্ম (বৈজ্ঞানিক নাম Spinochordodes tellinii) নামে এক ফিতাকৃমি সদৃশ প্যারাসাইট আছে যা ঘাসফড়িং-এর মস্তিষ্ককে সংক্রমিত করে ফেললে ঘাসফড়িং পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। এর ফলে নেমাটোমর্ফ হ্যেরওয়ার্মের প্রজননে সুবিধা হয়। অর্থাৎ নিজের প্রজননগত সুবিধা পেতে নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্ম বেচারা ঘাসফড়িংকে আত্মহত্যায় পরিচালিত করে[৩০৪]। এছাড়া জলাতঙ্ক রোগের সাথে আমরা সবাই কমবেশি পরিচিত। পাগলা কুকুর কামড়ালে আর উপযুক্ত চিকিৎসা না পেলে জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু মস্তিষ্ক অধিকার করে ফেলে। ফলে আক্রান্ত মস্তিষ্কের আচরণও পাগলা কুকুরের মতোই হয়ে ওঠে। আক্রান্ত ব্যক্তি অপরকে কামড়াতেও যায়। অর্থাৎ ভাইরাসের সংক্রমণে মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে।
আমাদের দীর্ঘদিনের জমে থাকা প্রথাগত বিশ্বাসের ভাইরাসগুলোও কি আমাদের এভাবে আমাদের অজান্তেই বিপথে চালিত করে না? আমরা আমাদের বিশ্বাস রষ্কার জন্য প্রাণ দেই, বিধর্মীদের হত্যা করি, টুইন টাওয়ারের ওপর হামলে পড়ি, সতী নারীদের পুড়িয়ে আত্মতৃপ্তি পাই, বেগানা মেয়েদের পাথর মারি। মনোবিজ্ঞানী ড্যারেল রে US ‘The God Virus : How religion infects our lives and culture’ বইয়ে বলেন, জলাতঙ্কের জীবাণু দেহের ভেতরে ঢুকলে যেমন মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বিকল হয়ে যায়, ঠিক তেমনই ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোও মানুষের চিন্তাচেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তৈরি হয় ভাইরাস আক্রান্ত মননের। ড্যারেল রে তার বইয়ে বলেন[৩০৫]–
Virtually all religion rely upon early childhood indoctrination as the prime infection strategy… Biological virus strategies bear a remarkable resemblance to method of religious propagation. Religious conversion seems to affect personally. In the viral paradigm, the God virus infects and takes over critical thinking capacity of individual with respect to his or her own religion, much as rabies affects specific parts of the central nervous system.
নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্ম যেমনিভাবে ঘাসফড়িংকে আত্মহত্যায় পরিচালিত করে, ঠিক তেমনই আমরা মনে করি ধর্মের বিভিন্ন বাণী এবং জিহাদি শিক্ষা মানবসমাজে অনেকসময়ই ভাইরাস কিংবা প্যারাসাইটের মতো সংক্রমণ ঘটিয়ে আত্মঘাতী করে তোলে। ফলে আক্রান্ত সন্ত্রাসী মনন বিমান নিয়ে আছড়ে পড়ে টুইন টাওয়ারের ওপর। নাইন ইলেভেনের বিমান হামলায় উনিশ জন ভাইরাস আক্রান্ত মনন ঈশ্বরের কাজ করছি এই প্যারাসাইটিক ধারণা মাথায় নিয়ে হত্যা করেছিল প্রায় তিন হাজার সাধারণ মানুষকে। ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগোর অধ্যাপক ব্রুস লিংকন, তার বই ‘হলি টেররস : থিংকিং অ্যাবাউট রিলিজিয়ন আফটার সেপ্টেম্বর ইলেভেন’ বইয়ে বিষয়টির ওপর আলোকপাত করে বলেন, ‘ধর্মই মুহাম্মদ আতাসহ আঠারো জনকে প্ররোচিত করেছিল এই বলে যে, সংগঠিত বিশাল হত্যাযজ্ঞ শুধু তাদের কর্তব্য নয়, বরং স্বর্গ থেকে আগত পবিত্র দায়িত্ব[৩০৬]। হিন্দু মৌলবাদীরাও একসময় ভারতে রামজন্মভূমির অতিকথনের ভাইরাস বুকে লালন করে ধ্বংস করেছে শতাব্দী প্রাচীন বাবরি মসজিদ। এধরনের অসংখ্য দৃষ্টান্ত ইতিহাস থেকে হাজির করা যাবে, ভাইরাস আক্রান্ত মনন কীভাবে কারণ হয়েছিল সভ্যতা ধ্বংসের।
ছবি। পেজ ৩৬০
চিত্র : বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, নেমাটোমর্ফ হেয়ারওয়ার্ম নামে এক প্যারাসাইটের সংক্রমণে ঘাসফড়িং পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে (বামে), ঠিক একইভাবে বিশ্বাসের ভাইরাসের সংক্রমণে আক্রান্ত আল কায়দার ১৯ জন সন্ত্রাসী যাত্রীবাহী বিমান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল টুইন টাওয়ারের ওপর ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর (ডানে)। বিশ্বাসের ভাইরাসের বাস্তব উদাহরণ।
১১ই সেপ্টেম্বরের সেই ঐতিহাসিক ঘটনার পরে অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স ফ্রি এনকোয়েরি পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন ‘Design for a Faith-Based Missile নামে। তিনি সেই প্রবন্ধে আত্মঘাতী সন্ত্রাসীদের বিশ্বাস নির্ভর (ভাইরাসাক্রান্ত) মিসাইল হিসেবে অভিহিত করে লেখেন[৩০৭]–
There is no doubt that the afterlife-obsessed suicidal brain really is a weapon of immense power and danger. It is comparable to a smart missile, and its guidance system is in many respects superior to the most sophisticated electronic brain that money can buy. Yet to a cynical government, organization, or priesthood, it is very very cheap.
২০১০ সালে প্রকাশিত বই ‘সমকামিতা : একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান’-এ দেখানো হয়েছে সমকামের প্রতি অহেতুক ঘৃণা-বিদ্বেষ তৈরিতেও ধর্মের বিশাল ভূমিকা আছে। প্রথম দিকের প্রাচীন জনগোষ্ঠীর মধ্যকার ধর্মগুলো এত প্রাতিষ্ঠানিক রূপে ছিল না বলে সমকামের প্রতি বিদ্বেষ এত তীব্রভাবে অনুভূত হয় নি। ধর্ম প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাওয়ার পর থেকেই পাদ্রি, পুরোহিত মোল্লারা ঢালাওভাবে সমকামিতাকে ‘ধর্মবিরুদ্ধ যৌনাচার’, ‘মহাপাপ’, ‘প্রকৃতিবিরুদ্ধ বিকৃতি’ প্রভৃতি হিসেবে আখ্যা দিতে শুরু করে এবং এর ধারাবাহিকতায় শুরু হয় পৃথিবী জুড়ে সমকামীদের ওপর লাগাতার নিগ্রহ এবং অত্যাচার[৩০৮]। এটাকে ভাইরাস আক্রান্ত মনন ছাড়া আর কী বলা যায়?
ইসলামি সন্ত্রাসবাদের বিষয়ে আবারও ফিরে তাকাই। ইসলামি সন্ত্রাসবাদ লালন-পালনে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার বিশাল অবদান আছে, এ কথা নিঃসন্দেহে সত্য। কিন্তু তারপরেও কেবল আমেরিকার দিকে অঙ্গুলি তুলে ধর্মগ্রন্থগুলোকে কখনোই ‘ধোয়া তুলসীপাতা’ বানানো যায় না। ধর্মগ্রন্থের যে অংশগুলোতে জিহাদের কথা আছে (২ : ২১৬, ২ : ১৫৪), উদ্ভিন্নযৌবনা হুরিদের কথা আছে (৫২ : ১৭-২০, ৪৪ : ৫১-৫৫, ৫৬ : ২২), ‘মুক্তা সদৃশ’ গেলমানদের কথা আছে (৫২ : ২৪, ৫৬ : ১৭, ৭৬ : ১৯) সেসমস্ত ‘পবিত্র বাণীগুলো ছোটবেলা থেকে মাথায় ঢুকিয়ে দিয়ে কিংবা বছরের পর বছর। সৌদি পেট্রোডলারে গড়ে ওঠা মাদ্রাসা নামক আগাছার চাষ করে বিভিন্ন দেশে তরুণ সমাজের কিছু অংশের মধ্যে এক ধরনের বিশ্বাসের ভাইরাস তৈরি করা হয়েছে। ফলে এই ভাইরাস-আক্রান্ত জিহাদিরা স্বর্গের ৭২টা হুর-পরীর আশায় নিজের বুকে বোমা বেঁধে আত্মাহুতি দিতেও আজ দ্বিধাবোধ করে না; ইহুদি, কাফের, নাসারাদের হত্যা করে ‘শহীদ’ হতে তারা কার্পণ্যবোধ করে না। ল্যাংসেট ফুক প্যারাসাইটের মতো তাদের মনও কেবল একটি বিশ্বাস দিয়ে চালিত অমুসলিম কাফেরদের হত্যা করে সারা পৃথিবীতে ইসলাম কায়েম করতে হবে, আর পরকালে পেতে হবে আল্লাহর কাছ থেকে উদ্ভিন্নযৌবনা আয়তলোচনা হুর পরীর লোভনীয় পুরস্কার। তারা ওই ভাইরাস আক্রান্ত পিঁপড়ার মতো হামলে পড়ছে কখনও টুইন টাওয়ারে, কখনও রমনার বটমূলে কিংবা তাজ হোটেলে।
কীভাবে বিশ্বাসের ক্ষতিকর ভাইরাসগুলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সঞ্চালিত হয়, তা বৈজ্ঞানিকভাবে বুঝতে হলে আমাদের জানতে হবে আধুনিক মিম তত্বকে। মিম নামের পরিভাষাটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন জীববিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স ১৯৭৬ সালে, তার বিখ্যাত বই ‘দ্য সেলফিশ জিন’-এ[৩০৯]। আমরা তো জিন-এর কথা ইদানীং অহরহ শুনি। জিন হচ্ছে মিউটেশন, পুনর্বিন্যাস ও শারীরবৃত্তিক কাজের জন্য আমাদের ক্রোমোজোমের ক্ষুদ্রতম অবিভাজ্য একক। সহজ কথায়, তিন জিনিসটা হচ্ছে শারীরবৃত্তীয় তথ্যের অখণ্ড একক যা বংশগতিয় তথ্যকে এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে ছড়িয়ে দেয়। জিন যেমন আমাদের শারীরবৃত্তীয় তথ্য বংশ পরম্পরায় বহন করে, ঠিক তেমনই সাংস্কৃতিক তথ্য বংশপরম্পরায় বহন করে নিয়ে যায় ‘মিম। কাজেই ‘মিম’ হচ্ছে আমাদের ‘সাংস্কৃতিক তথ্যের একক’, যা ক্রমিক অনুকরণ বা প্রতিলিপির মাধ্যমে একজনের মন থেকে মনান্তরে ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক যেভাবে শারীরবৃত্তীয় তথ্যের একক জিন ছড়িয়ে পড়ে এক শরীর থেকে অন্য শরীরে। যে ব্যক্তি মিমটি বহন করে তাদের মিমটির ‘হোস্ট’ বা বাহক বলা যায় ‘মিমপ্লেক্স’ হলো একসাথে বাহকের মনে অবস্থানকারী পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত একদল ‘মিম। কোনো বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাস, রীতি-নীতি, কোনো দেশীয় সাংস্কৃতিক বা কোনো রাজনৈতিক মতাদর্শ-এগুলো সবই মিমপ্লেক্সের উদাহরণ। সুজন ব্ল্যাকমোর তার ‘মিম মেশিন’ বইয়ে মিমপ্লেক্সের অনেক আকর্ষণীয় উদাহরণ হাজির করেছেন। সুজান ব্ল্যাকমোর মনে করেন জিন এবং মিমের সুগ্রন্থিত সংশ্লেষই মানুষের আচার ব্যবহার, পরার্থতা, যুদ্ধংদেহী মনোভাব, রীতি-নীতি কিংবা কুসংস্কারের অস্তিত্বকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। মিম নিয়ে মুক্তমনা সাইটে দিগন্ত সরকার বাংলায় চমৎকার একটি প্রবন্ধ লিখেছেন, সেটি রাখা আছে মুক্তমনায় প্রকাশিত ই-বই ‘বিজ্ঞান ও ধর্ম : সংঘাত নাকি সমন্বয়’-এ[৩১০]। এই ই-বইটিতে দিগন্ত সরকার ধর্মের উৎস সন্ধানে নামের বাংলা প্রবন্ধটিতে মিমবিন্যাসের আলোকে ধর্মের উৎপত্তির ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা মূলত ডকিন্স এবং সুজন ব্ল্যাকমোরের মিম নিয়ে আধুনিক চিন্তাধারারই অনিন্দ্যসুন্দর প্রকাশ[৩১১]। সম্প্রতি মুক্তমনা ব্লগে ব্লগার স্বাধীন একটি চমৎকার লেখা লিখেছেন ‘জিন এবং মিম’ শিরোনামে। তিনিও তার প্রবন্ধের মাধ্যমে মিমের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন বাঙালি পাঠকদের জন্য। এছাড়া অন্য বাংলা ব্লগগুলোতেও সম্প্রতি মিম নিয়ে ভালো লেখা উঠে আসছে।
কোনো সাংস্কৃতিক উপাদান কিংবা কোনো বিশেষ ধর্মীয় বিশ্বাস কীভাবে মিমের মাধ্যমে জনপুঞ্জে ছডিযে পড়ে? মানুষের মস্তিষ্ক এক্ষেত্রে আসলে কাজ করে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার যেভাবে কাজ করে অনেকটা সেরকমভাবে। আর মিমগুলো হচ্ছে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারের মধ্যে ইন্সটল করা সফটওয়্যার যেন। যতক্ষণ পর্যন্ত এই সফটওয়্যারগুলো ভালোমতো চলতে থাকে ততক্ষণ তা নিয়ে আমাদের কোনো চিন্তা থাকে না। কিন্তু কখনও কখনও কোনো কোনো সফটওয়্যার ভালো মানুষের (নাকি ‘ভালো মিমের’ বলা উচিত) ছদ্মবেশ নিয়ে ট্রোজান হর্স’ হয়ে ঢুকে পড়ে। এরাই আসলে বিশ্বাসের ক্ষতিকর ভাইরাসগুলো। এরা সুচ হয়ে ঢোকে, আর শেষ পর্যন্ত যেন ফাল হয়ে বেরোয়। যতক্ষণে এই ভাইরাসগুলোকে শনাক্ত করে নির্মূল করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়-ততক্ষণে আমাদের হার্ডওয়্যারের দফারফা সারা। এই বিশ্বাসের ভাইরাসের বলি হয়ে প্রাণ হারায় শত সহস্র মানুষ-কখনও নাইন-ইলেভেনে, কথনোবা বাবরি মসজিদ ধ্বংসে, কখনোবা তাজ হোটেলে গোলাগুলিতে। Viruses of the Mind শীর্ষক একটি গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে অধ্যাপক রিচার্ড ডকিন্স দেখিয়েছেন কীভাবে কম্পিউটার ভাইরাসগুলোর মতোই আপাত মধুর ধর্মীয় শিক্ষাগুলো সমাজের জন্য ট্রোজান হর্স কিংবা ওয়ার্ম ভাইরাস হিসেবে কাজ করে তিলে তিলে এর কাঠামোকে ধ্বংস করে ফেলতে চায়। আরও বিস্তৃতভাবে জানবার জন্য পাঠকেরা পড়তে পারেন সাম্প্রতিক সময়ে রিচার্ড ব্রডির লেখা ‘ভাইরাস অফ মাইন্ড কিংবা ক্রেগ জেমসের লেখা ‘দ্য রিলিজিয়ন ভাইরাস’ নামের বইগুলো[৩১২]। এ বইগুলো থেকে বোঝা যায় ভাইরাস আক্রান্ত মস্তিষ্ক কী শান্তভাবে রোবটের মতো ধর্মের আচার আচরণগুলো নির্দ্বিধায় পালন করে যায় দিনের পর দিন, আর কখনো-সখনো বিধর্মী নিধনে উন্মত্ত হয়ে ওঠে; একসময় দেখা দেয় আত্মঘাতী হামলা, জিহাদ কিংবা ক্রুসেডের মহামারী।
.
ভাইরাস আক্রান্ত মনন
ভাইরাস আক্রান্ত মন-মানসিকতার উদাহরণ আমাদের চারপাশেই আছে ঢের। কিছু উদাহরণ তো দেওয়াই যায়। এই ধরনের ভাইরাস-আক্রান্ত মননের সাথে বিতর্ক করার অভিজ্ঞতা এই বইয়ের দুজন লেখকেরই কম বেশি আছে। তার কিছু কিছু বর্ণনা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে (ধর্মীয় নৈতিকতা) রাখা হয়েছে। ব্লগ সাইটে বিতর্ক করতে গেলে ব্যাপারটা ভালো বোঝা যায়। আপনি যত ভালো যুক্তি দেন না কেন, পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, নৃতত্ব এবং সমাজবিজ্ঞান থেকে যত আধুনিক এবং অথেনটিক গবেষণারই উল্লেখ করুন না কেন, তারা চির আরাধ্য ধর্মগ্রন্থকে মাথায় করে রাখবেন আর আপনার প্রতি গালি গালাজের বন্যা বইয়ে দেবেন। এই ধরনের অভিজ্ঞতা শুধু আমাদের নয়, ইন্টারনেটে যারা বিজ্ঞান, যুক্তিবাদিতা, সংশয়বাদিতা প্রভৃতি নিয়ে লেখালেখি করেন সেরকম অনেক লেখকেরই আছে।
এই ভদ্রলোকেরা হত ভাইরাস আক্রান্ত মননের খুব ছোট উদাহরণ। কিন্তু ভাইরাস আক্রান্ত মননের চরম উদাহরণগুলো হাজির করলে বোঝা যাবে কীভাবে এ ধরনের মানসিকতাগুলো সমাজকে পঙ্গু করে দেয়, কিংবা কীভাবে সমাজের প্রগতিকে থামিয়ে দেয়। এর অজস্র উদাহরণ পৃথিবী জুড়ে পাওয়া যাবে। কিছু প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস থেকে জানা যায়, যখন কোনো নতুন প্রাসাদ কিংবা ইমারত তৈরি করা হতো, তার আগে সেই জায়গায় শিশুদের জীবন্ত কবর দেওয়া হতো-এই ধারণা থেকে যে, এটি প্রাসাদের ভিত্তি মজবুত করবে। অনেক আদিম সমাজেই বন্যা কিংবা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কুমারী উৎসর্গ করার বিধান ছিল; কেউ কেউ সদ্য জন্মলাভ করা শিশুদের হত্যা করত, এমনকি খেয়েও ফেলত। কোনো কোনো সংস্কৃতিতে কোনো বিখ্যাত মানুষ মারা গেলে অন্য মহিলা এবং পুরুষদেরও তার সাথে জীবন্ত কবর দেওয়া হতো, যাতে তারা পরকালে গিযে পুরুষটির কাজে আসতে পারে। ফিজিতে ‘ভাকাতোকা’ নামে এক ধরনের বীভৎস। রীতি প্রচলিত ছিল যেখানে একজনের হাত-পা কেটে ফেলে তাকে দেখিয়ে দেখিযে সেই কর্তিত অঙ্গগুলো খাওয়া হতো। আফ্রিকার বহু জাতিতে হত্যার রীতি চালু আছে মৃত–পূর্বপুরুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্য। এগুলো সবই মানুষ করেছে ধর্মীয় রীতি নীতিকে প্রাধান্য দিতে গিযে, অদৃশ্য ঈশ্বরকে তুষ্ট করতে গিযে। এধরনের ধর্মীয় হত্যা’ সম্বন্ধে আরও বিস্তৃতভাবে জানার জন্য ডেভিড নিগেলের ‘Human Sacrifice : In History And Today’ বইটি পড়া যেতে পারে। এগুলো সবই সমাজে বিশ্বাসের ভাইরাস’ নামক আগাছার চাষ ছাড়া আর কিছু নয়।
ইতিহাসের পরতে পরতে অজস্র উদাহরণ লুকিয়ে আছে কীভাবে বিশ্বাসের ভাইরাসগুলো আণবিক বোমার মতোই মারণাস্ত্র হিসেবে কাজ করে লক্ষ কোটি মানুষের প্রাণহানির কারণ হয়েছে। ধর্মযুদ্ধগুলোই তো এর বাস্তব প্রমাণ। কিছু নমুনা দেখা যাক[৩১৪]—
- ইতিহাসের প্রথম ক্রুসেড সংগঠিত হয়েছিল ১০৯৫ সালে। সেসময় ‘Deus Vult (ঈশ্বরের ইচ্ছা) ধ্বনি দিয়ে হাজার হাজার মানুষকে জার্মানির রাইন ভ্যালিতে হত্যা করা হয় এবং বাস্তুচ্যুত করা হয়। জেরুজালেমের প্রায় প্রতিটি অধিবাসীকে হত্যা করা হয় শহর পবিত্র করার নামে।
- দ্বিতীয় ক্রুসেড পরিচালনার সময় সেন্ট বার্নার্ড ফতোয়া দেন, ‘প্যাগানদের হত্যার মাধ্যমেই খ্রিস্টানদের গৌরব ফিরিয়ে আনা সম্ভব।
- প্রাচীন আরবে ‘জামালের যুদ্ধে প্রায় দশ হাজার মুসলিম নিহত হয়েছিল, তাদের আপন জ্ঞাতিভাই মুসলিমদের দ্বারাই। ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মুহাম্মদ নিজেও বনি কুরাইজার ৭০০ বন্দিকে একসাথে হত্যা করেছিলেন। বলে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে।
- বাইবেল থেকে (নাম্বারস ৩১ : ১৬-১৮) জানা যায়, মুসা প্রায় এক লক্ষ পুরুষ এবং আটষট্টি হাজার অসহায় নারী হত্যা করেছিলেন।
- রামায়ণে রাম তার তথাকথিত ‘রাম রাজ্যে’ শম্বুককে হত্যা করেছিলেন বেদ পাঠ করার অপরাধে।
- প্রাচীন মায়া সভ্যতায় নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। অদৃশ্য ঈশ্বরকে তুষ্ট করতে গিয়ে হাজার হাজার মানুষকে মাথা কেটে ফেলে, হৃৎপিণ্ড উপড়ে ফেলে, অন্ধকূপে ঠেলে ফেলে দিয়ে হত্যা করা হতো। ১৪৪৭ সালে গ্রেট পিরামিড অফ টেনোখটিটলান তৈরির সময় চার দিনে প্রায় ৮০,৪০০ বন্দিকে ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করা হয়েছিল। শুধু মায়া। সভ্যতাতে নয় সারা পৃথিবীতেই এধরনের উদাহরণ আছে। পেরুতে প্রি-ইনকা উপজাতিরা হাউজ অব দ্য মুন’ মন্দিরে শিশুদের হত্যা করত। তিব্বতে বন শাহমানেরা ধর্মীয় রীতির কারণে মানুষ হত্যা করত। বোর্নিওতে বাড়ির ইমারত বানানোর আগে প্রথম গাঁথুনিটা এক কুমারীর দেহ দিয়ে প্রবেশ করানো হতো ‘ভূমিদেবতা’-কে তুষ্ট করার খাতিরে। প্রাচীন ভারতে দ্রাবিড়রা গ্রামের ঈশ্বরের নামে মানুষ উৎসর্গ করত। কালিভক্তরা প্রতি শুক্রবারে শিশুবলি দিত।
- তৃতীয় ক্রুসেডে রিচার্ডের আদেশে তিন হাজার বন্দিকে যাদের অধিকাংশই ছিলেন নারী এবং শিশু জবাই করে। হত্যা করা হয়। ইসমাইলি শিয়া মুসলিমদের একটি অংশ একসময় লুকিয়ে ছাপিয়ে বিধর্মী প্রতিপক্ষদের হত্যা করত। এগারো থেকে তেরো শতক পর্যন্ত আধুনিক ইরান, ইরাক এবং সিরিয়ায় বহু নেতা তাদের হাতে প্রাণ হারায়। শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের আরেক দস্যুদল মোঙ্গলদের হাতে তাদের উচ্ছেদ ঘটে-কিন্তু তাদের বীভৎস কীর্তি আজও অম্লান।
- কথিত আছে, এগারো শতকের শুরুর দিকে ইহুদিরা খ্রিস্টান শিশুদের ধরে নিয়ে যেত, তারপর উৎসর্গ করে তাদের রক্ত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ব্যবহার করত। এই রক্তের মহাকাব্য রচিত হয়েছে এমনই ধরনের শত সহস্র অমানবিক ঘটনার ওপর ভিত্তি করে।
- ১২০৯ সালে পোপ তৃতীয় ইনোসেন্ট উত্তর ফ্রান্সের আলবিজেনসীয় খ্রিস্টানদের ওপর আক্ষরিক অর্থেই ক্রুসেড চালিয়েছিলেন। শহর দখল করার পর যখন সৈন্যরা ঊর্ধ্বতনদের কাছ থেকে পরামর্শ চেয়েছিল কীভাবে বন্দিদের মধ্যে থেকে বিশ্বাসী এবং অধার্মিকদের মধ্যে পার্থক্য করা যাবে। পোপ তখন আদেশ দিয়েছিলেন ‘সবাইকে হত্যা করো। পোপের আদেশে প্রায় বিশ হাজার বন্দিকে চোখ বন্ধ করে ঘোড়ার পেছনে দড়ি দিয়ে বেঁধে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়।
- মুসলিমদের পবিত্র যুদ্ধ ‘জিহাদ উত্তর আফ্রিকা থেকে শুরু করে স্পেন পর্যন্ত রক্তাক্ত করে তোলে। তারপর এই জিহাদের মড়ক প্রবেশ করে ভারতে। তারপর চলে যায় বলকান (ক্যাথলিক ক্রোয়েশিয়া, অর্থোডক্স সার্ব এবং মুসলিম বসনিয়ান এবং কসোভা) থেকে অস্ট্রিয়া পর্যন্ত।
- বারো শতকের দিকে ইনকারা পেরুতে তাদের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে, যে সাম্রাজ্যের পুরোধা ছিলেন একদল পুরোহিত। তারা ঈশ্বর-কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে ২০০ শিশুকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে।
- ১২১৫ সালের দিকে চতুর্থ ল্যাটেরিয়ান কাউন্সিল ঘোষণা করে, তাদের বিস্কুটগুলো (host wafer) নাকি অলৌকিকভাবে যিশুর দেহে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। এরপর একটি গুজব রটিয়ে দেওয়া হয় যে, ইহুদিরা নাকি সেসব পবিত্র বিস্কুট চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে। এই গুজবের ওপর ভিত্তি করে ১২৪৩ সালের দিকে অসংখ্য ইহুদিকে জার্মানিতে হত্যা করা হয়। একটি রিপোর্টে দেখা যায়, ছয় মাসে ১৪৬ জন ইহুদিকে হত্যা করা হয়েছিল। এই ‘পবিত্র হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকে প্রায় ১৮ শতক পর্যন্ত।
- বারো শতকের দিকে ইউরোপ জুড়ে আলবেজেনসীয় ধর্মদ্রোহীদের খুঁজে খুঁজে হত্যার রীতি চালু হয়। ধর্মদ্রোহীদের কখনও পুডিযে, কখনও ধারালো অস্ত্র দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে, কখনোবা শিরচ্ছেদ করে হত্যা করা হয়। পোপ চতুর্থ ইনোসেন্ট এই সমস্ত হত্যায় প্রত্যক্ষ ইন্ধন যুগিয়েছিলেন। কথিত আছে ধর্মবিচরণ সভার সংবীক্ষক (Inquisitor) রবার্ট লি বোর্জে এক সপ্তাহে ১৮৩ জন ধর্মদ্রোহীকে হত্যার জন্য পাঠিয়েছিলেন।
- বহু লোক সেসময় নিপীড়ন থেকে বাঁচতে ধর্মত্যাগ করেন, কিন্তু সেসমস্ত ধর্মত্যাগীকে পুরনো ধর্মের অবমাননার অজুহাতে হত্যার আদেশ দেওয়া হয়। স্পেনে প্রায় ২০০০ ধর্মত্যাগীকে পুড়িয়ে মারা হয়। কেউ কেউ ধর্মত্যাগ না করলেও ধর্মের অবমাননার অজুহাতে পোড়ানো হয়। জিওর্দানো ব্রুনোর মতো দার্শনিককে বাইবেল-বিরোধী কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক তত্ব সমর্থন করার অপরাধে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয় সেসময়।
- ইতিহাস খ্যাত ‘ব্ল্যাক ডেথ’ যখন সারা ইউরোপে ১৩৪৮-১৩৪৯-এ ছড়িয়ে পড়েছিল, গুজব ছড়ানো হয়েছিল এই বলে যে, ইহুদিরা কুয়ার জল কিছু মিশিয়ে বিষাক্ত করে দেওয়ায় এমনটি ঘটছে। বহু ইহুদিকে এ সময় সন্দেহের বশে জবাই করে হত্যা করা হয়। জার্মানিতে পোড়ানো দেহগুলোকে স্থূপ করে মদের বড় বড় বাক্সে ভরে ফেলা হয় এবং রাইন নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। উত্তর জার্মানিতে ইহুদিদের ছোট্ট কুঠরিতে গাদাগাদি করে রাখা হয় যেন তারা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়, কখনোবা তাদের পিঠে চাবুক কষা হয়। থারিজিয়ার যুবরাজ জনসমক্ষে ঘোষণা করেন যে, তিনি তার ইহুদি ভৃত্যকে ঈশ্বরের নামে হত্যা করেছেন; অন্যদেরকেও তিনি একই কাজে উৎসাহিত করেন।
- তেরো শতকে অ্যাজটেক সভ্যতা যখন বিস্তার লাভ করেছিল, নরবলি প্রথার বীভৎসতার তখন স্বর্ণযুগ। প্রতি বছর প্রায় বিশ হাজার লোককে ঈশ্বরের নামে উৎসর্গ করা হতো। তাদের সূর্যদেবের নাকি দৈনিক ‘পুষ্টির জন্য মানব রক্তের খুব দরকার পড়তো। বন্দিদের কখনও শিরচ্ছেদ করা হতো, এমনকি কোনো কোনো অনুষ্ঠানে তাদের দেহ টুকরো টুকরো করে ভক্ষণ করা হতো। কখনোবা পুড়িয়ে মারা হতো, কিংবা উঁচু জায়গা থেকে ফেলে দেওয়া হতো। বর্ণিত আছে, তাদের একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এক অক্ষতযোনি কুমারীকে দিয়ে ২৪ ঘণ্টা ধরে নাচানো হয়, তারপর তার গায়ের চামড়া তুলে ফেলে পুরোহিত তা পরিধান করেন। তারপর আরও ২৪ ঘণ্টা ধরে নাচতে থাকেন। রাজা আহুইতজোলের রাজাভিষেকে আশি হাজার বন্দিকে শিরচ্ছেদ করে ঈশ্বরকে তুষ্ট করা হয়।
- ১৪০০ সালের দিকে ধর্মদ্রোহীদের থেকে চাচের দৃষ্টি চলে যায় উইচক্র্যাফটের দিকে। চার্চের নির্দেশে হাজার হাজার নারীকে ‘ডাইনি’ সাব্যস্ত করে পুড়িয়ে মারা শুরু হয়। এই ডাইনি পোড়ানোর রীতি এক ডজনেরও বেশি দেশে একেবারে গণহিস্টেরিয়ায় রূপ নেয়। সেসময় কতজনকে এরকম ডাইনি বানিয়ে পোড়ানো হয়েছে? সংখ্যাটা এক লক্ষ থেকে শুরু করে ২০ লক্ষ ছাড়িয়ে যেতে পারে। ঠগ বাছতে গা উজাড়ের মতোই ডাইনি বাছতে গিয়ে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় করে দেওয়া হয়েছে। সতের শতকের প্রথমার্ধে অ্যালজাস (Alsace) নামের ফরাসি প্রদেশে ৫০০০ ডাইনিকে হত্যা করা হয়, ব্যাম্বার্গের ব্যাভারিয়ান নগরীতে ৯০০ জনকে পুড়িয়ে মারা হয়। ডাইনি পোড়ানোকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট ধর্মীয় উন্মত্ততা সেসময় অতীতের সমস্ত রেকর্ডকে ম্লান করে দেয়।
- সংখ্যালঘু প্রোটেস্ট্যান্ট হুগেনটস ১৫০০ সালের দিকে ফ্রান্সের ক্যাথলিক খ্রিস্টানদের দ্বারা নির্মম নিপীড়নের শিকার হয়। ১৫৭২ সালে সেন্ট বার্থোলোমিও দিবসে ক্যাথরিন দ্য মেদিসিস গোপনে তাদের ক্যাথলিক সৈন্য হুগেটসের বসতিতে প্রেরণ করে আক্ষরিক অর্থেই তাদের কচুকাটা করে। প্রায় ছয় সপ্তাহ ধরে এই হত্যাযজ্ঞ চলতে থাকে আর এতে প্রাণ হারায় অন্তত দশ হাজার হুগেটস। হুগেনটসদের ওপর সংখ্যাগুরু খ্রিস্টানদের আক্রোশ পরবর্তী দুই শতক ধরে অব্যাহত থাকে। ১৫৬৫ সালের দিকে একটি ঘটনায় হুগেটসের একটি দল ফ্লোরিডা পালিয়ে যাওয়ার সময় স্প্যানিশ বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে তাদের এলাকার সবাইকে ধরে ধরে হত্যা করা হয়।
- আবার ওদিকে পনেরো শতকে ভারতে কালীভক্ত কাপালিকের দল মা কালীকে তুষ্ট করতে গিয়ে অন্যদের শ্বাসরোধ আর জবাই করে হত্যা করত। এই কুৎসিত রীতির বলি হয়ে প্রাণ হারায় প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ। এখনও কিছু মন্দিরে বলি দেওয়ার রীতি চালু আছে। তবে আধুনিক রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের গ্যাঁড়াকলে পড়ে ব্রাহ্মণ-পুরোহিতরা আর আগের মতো মানুষকে বলি দিতে পারে না সেই আক্রোশ প্রতিফলিত হয় নিরীহ পাঠার ওপর দিয়ে দুধের স্বাদ ঘোলে মিটিযেই আধুনিক যুগে এভাবে রক্তলোলুপ মা কালীকে তুষ্ট রাখা হয়।
- ১৫৪৩ সালে ভিয়েনায় ১৬ বছরের একটা মেয়ের পেট ব্যথা শুরু হলে যিশুভক্তের দল তার ওপর আট সপ্তাহ ধরে এক্সরসিজম বা ওঝাগিরি শুরু করে। এই যিশুভক্ত পাদ্রির দল ঘোষণা করেন যে, তারা মেয়েটির দেহ থেকে ১২,৬৫২টা শয়তান তাড়াতে সক্ষম হয়েছেন। পাদ্রির দল ঘোষণা করে যে, মেয়েটির দাদী কাঁচের জারে মাছির অবয়বে শয়তান পুষতেন। সেই শয়তানের কারণেই মেয়েটার পেটে ব্যথা হতো। দাদীকে ধরে নির্যাতন করতে করতে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয় যে দাদী আসলে ডাইনি, শয়তানের সাথে নিয়মিত সেক্স করেন তিনি। অতঃপর দাদীকে ডাইনি হিসেবে সাব্যস্ত করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়। এটি তিন শতক ধরে ডাইনি পোড়ানোর নামে যে লক্ষ লক্ষ মহিলাকে পোড়ানো হয়েছিল, তার সামান্য একটি নমুনামাত্র।
- এনাব্যাপ্টিস্টরা এক সময় ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট অথোরিটিদের দ্বারা স্রেফ কচুকাটা হয়েছিলেন। জার্মানির মুন্সটারে এনাব্যাপ্টিস্টরা এক সময় শহরের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় আর নতুন জিয়ন’ প্রতিষ্ঠা করে ফেলে। ওদিকে আবার পাদ্রি মোল্লারা এনাব্যাপ্টিস্টদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম গড়ে তোলে এবং শহরের পতনের পর এনাব্যাপ্টিস্ট নেতাদের হত্যা করে চার্চের চূড়ায় ঝুলিয়ে রাখা হয়।
- প্রোটেস্ট্যান্ট এবং ক্যাথলিকদের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ১৬১৮ সালে শুরু হয়ে ত্রিশ বছর যাবত চলে। এ সময় পুরো মধ্য ইউরোপ পরিণত হয়েছিল বধ্যভূমিতে। জার্মানির জনসংখ্যা ১৮ মিলিয়ন থেকে ৪ মিলিয়নে নেমে আসে। আরেকটি হিসাব মতে, জনসংখ্যার প্রায় ত্রিশ ভাগ (এবং পুরুষদের পঞ্চাশ ভাগ) এ সময় নিহত হয়েছিল।
- ইসলামের জিহাদের নামে গত বারো শতক ধরে সারা পৃথিবীতে মিলিয়নের উপর মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। প্রথম বছরগুলোতে মুসলিম বাহিনী খুব দ্রুতগতিতে পূর্ব ভারত থেকে পশ্চিম মরক্কো পর্যন্ত আগ্রাসন চালায়। শুধু বিধর্মীদেরই হত্যা করে নি, নিজেদের মধ্যেও কোন্দল করে নানা দল-উপদল তৈরি করেছিল। কারিজিরা যুদ্ধ শুরু করেছিল সুন্নিদের বিরুদ্ধে। আজারিকিরা অন্য ‘পাপীদের’ মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল। ১৮০৪ সালে উসমান দান ফোডিও, সুদানের পবিত্র সত্ত্বা, গোবির সুলতানের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ শুরু করে। ১৯৫০ সালে আরেক সুদানীয় সুফি উমর-আল হজ্জ প্যাগান আফ্রিকান গোত্রের ওপরে নৃশংস বর্বরতা চালায়-গণহত্যা এবং শিরচ্ছেদ করে ৩০০ জন বন্দির ওপর। ১৯৮০ সালে তৃতীয় সুদানীয় ‘হলি ম্যান’ মুহাম্মদ আহমেদ জিহাদ চালিয়ে ১০,০০০ মিশরীয় হত্যা করে।
- ১৮০১ সালে রোমানিয়ার পাদ্রিরা ইহুদিদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে ১২৪ জন ইহুদিকে হত্যা করে।
- ভারতে ১৮১৫ থেকে ১৮২৮ সালের মধ্যে ৪১৩৫ নারীকে সতীদাহের নামে পুড়িয়ে হত্যা করা হয় (প্রতিবছর হত্যা করা হয় গড়ে ৫০৭ থেকে ৫৬৭ জনকে)।
- ১৮৪৪ সালে পার্শিয়ায় বাহাই ধর্মপ্রচার শুরু হলে কট্টরপন্থী ইসলামিস্টরা এদের ওপর চড়াও হয়। বাহাই ধর্মের প্রবর্তককে বন্দি এবং শেষ পর্যন্ত হত্যা করা হয়। দুই বছরের মধ্যে সেখানকার মৌলবাদী সরকার ২০,০০০ বাহাইকে হত্যা করে। তেহরানের রাস্তাঘাট আক্ষরিক অর্থেই রক্তের বন্যায় ভেসে যায়।
- বার্মায় ১৮৫০ সাল পর্যন্ত মানুষকে বলি দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। যখন রাজধানী মান্দালায় সরিয়ে নেওয়া হয়, তখন নগর রক্ষা করার জন্য ৫৬ জন নিষ্কলুষ’ লোককে প্রাচীরের নিচে পুঁতে ফেলা হয়। রাজ জ্যোতিষীরা ফতোয়া দেয় যে নগর বাঁচাতে হলে আরও ৫০০ জন নারী, পুরুষ এবং শিশু বলি দিতে হবে। সেই ফতোয়া অনুযায়ী বলি দেওয়া শুরু হয় এবং ১০০ জনকে বলি দেওয়ার পর ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপে সেই বলিপ্রথা রদ করা হয়। ১৮৫৭ সালে উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসনামলে এনফিল্ড রাইফেলের কান্ট্রিজ, যেটাতে শুয়োর আর গরুর চর্বি লাগানো ছিল বলে গুজব রটানো হয়, তাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা শুরু হয় এবং নির্বিচারে বহু লোককে হত্যা করা হয়।
- ১৯০০ সালে তুর্কি মুসলিমেরা খ্রিস্টান আর্মেনিয়ানদের ওপর নির্বিচারে গণহত্যা চালায়।
- ১৯২০ সালে ক্রিস্টেরো যুদ্ধে ৯০ হাজার মেক্সিকান মৃত্যুবরণ করে।
- ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগকে কেন্দ্র করে দাঙ্গায় প্রায় ১ মিলিয়ন লোক মারা যায়। এমনকি ‘মহাত্মা গান্ধীও দাঙ্গা রোধ করতে সফল হন নি, এবং তাকেও বেঘোরে হিন্দু ফ্যানাটিক নথুরাম গডসের হাতে মৃত্যুবরণ করতে হয়।
- ১৯৫০ থেকে ১৯৬০ সালের মধ্যে খ্রিস্টান, এনিমিস্ট এবং মুসলিমদের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে ৫০০,০০০ লোক মারা যায়।
- ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের ওপর গণহত্যা চালায়, নয় মাসে তারা প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ হত্যা করে, ধর্ষণ করে ২ লক্ষ নারীকে। যদিও এই যুদ্ধের পেছনে মদদ ছিল রাজনৈতিক, তারপরেও ধর্মীয় ব্যাপারটিও উপেক্ষণীয় নয়। পশ্চিম পাকিস্তানিদের বরাবরই অভিযোগ ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানিরা ‘ভালো মুসলমান’ নয়, এবং তারা ভারতের দালাল।
- ১৯৭৮ সালে গায়ানার জোন্সটাউনে রেভারেন্ড জিম জোন্স সেখানে ভ্রমণরত কংগ্রেসম্যান এবং তিন জন সাংবাদিককে হত্যার পর ৯০০ জনকে নিয়ে আত্মহত্যা করে, যা সারা পৃথিবীকে স্তম্ভিত করে দেয়।
- ইসলামি আইন মোতাবেক চুরির শাস্তি হিসেবে হাত কেটে ফেলার রেওয়াজ প্রচলিত আছে। সুদানে ১৯৮৩ থেকে ১৯৪৪ সালের মধ্যে প্রায় ৬৬ জনকে ধরে প্রকাশ্যে হাত কেটে ফেলা হয়। মডারেট মুসলিম নেতা মোহাম্মদ তাহাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মেরে ফেলা হয় কারণ তিনি হাত কেটে ফেলার মতো বর্বরতার প্রতিবাদ করেছিলেন।
- সৌদি আরবে ১৯৭৭ সালে কিশোরী প্রিন্সেস এবং তার প্রেমিককে ‘ব্যভিচারের অপরাধে হত্যা করা হয়। পাকিস্তানে ১৯৮৭ সালে এক কাঠুরিয়ার মেয়েকে জেনা’ করার অপরাধে পাথর ছুঁড়ে হত্যার ফতোয়া দেওয়া হয়। ১৯৮৪ সালে আরব আমিরাতে একটি বাড়ির গৃহভৃত্য এবং দাসীকে পাথর ছুঁড়ে হত্যার ফতোয়া দেওয়া হয়, অবৈধ মেলামেশার অপরাধে।
- নাইজেরিয়ায় ১৯৮২ সালে মাল্লাম মারোয়ার ফ্যানাটিক অনুসারীরা প্রতিপক্ষের শতাধিক লোকজনকে ‘কাফের আখ্যা দিয়ে হত্যা করে, আর তাদের রক্তপান করে।
- ১৯৮৩ সালে উত্তর আয়ারল্যান্ডে ক্যাথলিক সন্ত্রাসীরা প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চে ঢুকে গোলাগুলি করে প্রোটেস্ট্যান্ট অনুসারীদের হত্যা করে। দাঙ্গায় প্রায় ২৬০০ লোক মারা যায়।
- হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা ভারতে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ১৯৮৩ সালে আসামে এরকম একটি দাঙ্গায় ৩,০০০ জন মানুষ মারা যায়। ১৯৪৪ সালে এক হিন্দু নেতার ছবিতে কোনো এক মুসলিম জুতার মালা পরিয়ে দিলে এ নিয়ে পুনরায় দাঙ্গা শুরু হয়। সেই দাঙ্গায় ২১৬ জন মারা যায়, ৭৫৬ জন আহত হয়, আর ১৩,০০০ জন উদ্বাস্তু হয়। কারাবন্দী হয় ৪১০০ জন।
- লেবাননে ১৯৭৫ সালের পর থেকে সুইসাইড বোম্বিংসহ নানা সন্ত্রাসবাদী ঘটনায় ১৩০,০০০ জন লোক মারা গেছে।
- ইরানের মৌলবাদী শিয়া সরকার ঘোষণা করে, যে সমস্ত বাহাই ধর্মান্তরিত না হবে, তাদের হত্যা করা হবে। ১৯৮০ সালের প্রথম দিকে প্রায় ২০০ জন ‘গোঁয়ার’ বাহাইকে হত্যা করা হয়, প্রায় ৪০,০০০ বাহাই দেশ ছেড়ে পালায়।
- শ্রীলঙ্কা বিগত শতকের আশি আর নব্বইয়ের দশকে বৌদ্ধ সিংহলী আর হিন্দু তামিলদের লড়াইযে আক্ষরিক অর্থেই নরকে পরিণত হয়।
- ১৯৮৩ সালে জেরুজালেমের ধর্মীয় নেতা মুফতি শেখ সাদ-ই-দীন এল আলামী ফতোয়া দেন এই বলে যে, কেউ যদি সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল আজাদকে হত্যা করতে পারে, তবে তার বেহেস্ত নিশ্চিত।
- ভারতে আশির দশকে শিখ জনগোষ্ঠী নিজেদের জন্য পাঞ্জাব এলাকায় আলাদা ধর্মীয় রাজ্য খালিস্তান’ (Land of the Pure) তৈরির পায়তারা করে আর এর নেতৃত্ব দেয় শিখ চরমপন্থি নেতা জারনাইন ভিন্দ্রানওয়ালা, যিনি তার অনুসারীদের শিখিয়েছিলেন যে, প্রতিপক্ষকে নরকে পাঠানো তাদের পবিত্র দায়িত্ব। চোরাগোপ্তা ভাবে পুরো আশির দশক জুড়েই বহু হিন্দুকে হত্যা করা হয়।
- ১৯৮৪ সালে শিখ দেহরক্ষীদের হাতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী নিহত হলে ভারত জুড়ে শিখদের ওপর বীভৎস তাণ্ডবলীলা চালানো হয়। তিন দিনের মধ্যে ৫০০০ শিখকে হত্যা করা হয়। শিখদের বাসা থেকে উঠিযে, বাস থেকে নামিয়ে, দোকান থেকে তুলে নিয়ে হত্যা করা হয়, কখনও জীবন্ত পুড়িয়ে দেওয়া হয়।
- ১৯৮৯ সালে ‘স্যাটানিক ভার্সেস” নামের উপন্যাস লেখার দায়ে সালমান রুশদিকে ফতোয়া দেওয়া হয় ইরানের ধর্মগুরু আয়াতোল্লা খোমেনির পক্ষ থেকে। বইটি না পডেই মুসলিম বিশ্বে রাতারাতি শুরু হয় জ্বালাও পোড়াও তাণ্ডব। ইসলামকে অবমাননা করে লেখার দায়ে এর আগেও মনসুর আল হাল্লাজ, আলী দাস্তি, আজিজ নেসিন, উইলিয়াম নেগার্ড, নাগিব মাহফুজ, তসলিমা নাসরিন, ড. ইউনুস শায়িখ, রবার্ট হুসেইন, হুমায়ুন আজাদ, আযান আরসি আলীসহ অনেকেই মৃত্যু পরোয়ানা পেয়েছেন। এদের মধ্যে অনেককেই মেরে ফেলা হয়েছে, কেউবা হয়েছেন পলাতক।
- ১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর রামজন্মভূমি’ মিথকে কেন্দ্র করে হিন্দু উগ্রপন্থীরা শত বছরের পুরনো বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে। এর ফলে দাঙ্গায় ২০০০ মানুষ মারা যায়, এর প্রভাব পড়ে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতেও।
- ১৯৯৭ সালে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় স্বর্গের দ্বার (Heaven’s Gate) নামে এক ‘ইউএফও ধর্মীয় সংগঠনের ৩৯ জন সদস্য একযোগে আত্মহত্যা করে, জীবনের ‘পরবর্তী স্তরে যাওয়ার লক্ষ্যে।
- বাংলাদেশে ১৯৪১ সালে হিন্দু জনসংখ্যা ছিল শতকরা ২৮ ভাগ। ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের অব্যবহিত পরে তা শতকরা ২২ ভাগে এসে দাঁড়ায়। এরপর থেকেই সংখ্যালঘুদের ওপর ক্রমাগত অত্যাচার এবং নিপীড়নের ধারাবাহিকতায় দেশটিতে ক্রমশ হিন্দুদের সংখ্যা কমতে থাকে। ১৯৬১ সালে ১৮.৫%, ১৯৭৪ সালে কমে দাঁড়ায় ১৩.৫%, ১৯৮১ সালে ১২.১%, এবং ১৯৯১ সালে ১০% এ এসে দাঁড়ায়। সাম্প্রতিক সময়গুলোতে হিন্দুদের শতকরা হার কমে ৮ ভগের নিচে নেমে এসেছে বলে অনুমিত হয়।
- ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার টুইন টাওয়ারের ওপর আল কায়দা আত্মঘাতী বিমান হামলা। চালায়। এই হামলায় টুইন টাওয়ার ধ্বসে পড়ে। মারা যায় ৩০০০ আমেরিকান নাগরিক। এ ভয়াবহ ঘটনা সারা বিশ্বের গতি-প্রকৃতিকে বদলে দেয়।
- ২০০২ সালে ভারতের গুজরাটে দাঙ্গায় ২০০০ মানুষ। মারা যায়, উদ্বাস্তু হয় প্রায় ১৫০,০০০ মানুষ। নারী নির্যাতন প্রকট আকার ধারণ করে। বহু মুসলিম কিশোরী এবং নারীকে উপর্যুপরি ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়।
- ২০০১ সালের নির্বাচনের পর বাংলাদেশে বিএনপি জামাত বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। নির্বাচন পরবর্তী সময়ে বেছে বেছে হিন্দুবাডিগুলোতে আক্রমণ চালানো হয়। পূর্ণিমা রানীর মতো বহু কিশোরীকে ধর্ষণ করা হয়। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রথম ৯২ দিনের মধ্যে ২২৮টি ধর্ষণের ঘটনা, এবং পরবর্তী তিন মাসে প্রায় ১০০০টি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে, যার মধ্যে শতকরা ৯৮ ভাগ ছিল হিন্দু কিংবা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত।
- বিএনপি-জামাত কোয়ালিশন সরকারের সময় বাংলা ভাইযের নেতৃত্বে জাগ্রত মুসলিম জনতার (জে. এম.জে.) উত্থান ঘটে। তারা পুলিশের ছত্রছায়ায় বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। একটি ঘটনায় একজন গ্রামবাসীকে হত্যা করে গাছের সাথে উল্টো করে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। সরকারের পক্ষ থেকে বাংলা ভাই মিডিয়ার সৃষ্টি বলে মিথ্যা প্রচারণা চালানো হয়।
- ২০০৪ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের প্রথা বিরোধী লেখক হুমায়ুন আজাদের উপর হামলা চালায় মৌলবাদী একটি দল। চাপাতি দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলা হয় তার দেহ, যা পরে তাকে প্রলম্বিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়।
- ২০০৪ সালের ২রা নভেম্বর চিত্র পরিচালক থিও ভ্যান গগকে প্রকাশ্যে রাস্তায় গুলি এবং ছুরিকাহত করে হত্যা করে সন্ত্রাসী মোহাম্মদ রোয়েরি। সাবমিশন নামের দশ মিনিটের একটি ইসলাম বিরোধী’ চলচ্চিত্র বানানোর দাযে তাকে নেদারল্যান্ডসের রাস্তায় প্রকাশ্যে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। একই ছবির সাথে জড়িত থাকার কারণে নারীবাদী লেখিকা আযান হারসি আলীকেও মৃত্যু পরোয়ানা দেওয়া হয়।
- ২০০৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর জেলেন্ডস পোস্টেন নামের একটি ড্যানিশ পত্রিকা মহানবী হজরত মুহাম্মদকে নিয়ে ব্যঙ্গাত্মক ১২টি কার্টুন প্রকাশ করলে সারা মুসলিম বিশ্বে এর প্রতিক্র্যিাস্বরূপ জ্বালাও-পোড়াও শুরু হয়। পাকিস্তানের এক ইমাম কার্টুনিস্টের মাথার দাম ধার্য করে এক মিলিয়ন ডলার। সিরিয়া, লেবানন, ইরান, পাকিস্তান, বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীতে সহিংসতায় মারা যায় শতাধিক লোক। ব্রিটেনের মুসলিমেরা ব্যানার নিয়ে Papo PS-’Behead those who say Islam is a violent religion’!
- ১৯৯৩ থেকে আজ পর্যন্ত ‘আর্মি অব গড’ সহ অন্যান্য গর্ভপাত-বিরোধী খ্রিস্টান মৌলবাদীরা আট জন ডাক্তারকে হত্যা করেছে। এই ধরনের নৃশংসতার সর্বশেষ নিদর্শন ২০০৯ সালে খ্রিস্টান মৌলবাদী স্কট রোডার কর্তৃক ড. জর্জ ট্রিলারকে হত্যা ন্যাশনাল অ্যাবরশন ফেডারেশনের সরবরাহকৃত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৭৭ সালের পর থেকে আমেরিকা এবং কানাডায় গর্ভপাতের সাথে জড়িত চিকিৎসকদের মধ্যে ১৭ জনকে হত্যার প্রচেষ্টা চলানো হয়, ৩৮৩ জনকে হত্যার হুমকি দেওয়া হয়, ১৫৩ জনের উপর চড়াও হওয়ার এবং ৩ জনকে অপহরণের ঘটনা ঘটে।
- বাংলাদেশে বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে সামান্য ‘মোহাম্মদ বিড়াল’ নিয়ে কৌতুকের জের হিসেবে ২১ বছর বয়সী কার্টুনিস্ট আরিফকে জেলে ঢোকানো হয়, বায়তুল মোকারমের খতিবের কাছে গিয়ে প্রথম আলোর সম্পাদকের ক্ষমা প্রার্থনার নাটক প্রদর্শিত হয়।
- আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগার অজুহাতে ফেসবুক বন্ধ করে দেওয়ার অপচেষ্টা করা হয়।
- ২০১৩ সালে শাহবাগ আন্দোলনের উত্তাল সময়ে রাজীব হায়দার শোভন, যিনি থাবা বাবা নামে ব্লগিং করতেন, তাকে জবাই করে হত্যা করা হয়। ধৃত অপরাধীরা স্বীকার করে ঈমানী দায়িত্ব পালনের জন্য ইসলামবিদ্বেষী এই ব্লগারকে তারা হত্যা করেছে।
- ধর্মবাদী দল হেফাজতে ইসলামের চাপে মুক্তচিন্তার ব্লগারদের গ্রেফতার করে বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালের পয়লা এপ্রিল। সুব্রত শুভ, মশিউর রহমান বিপ্লব এবং রাসেল পারভেজকে দাগী অপরাধীর মতো হাতকড়া পরিয়ে হাজির করা হয়। এর পর দিন আসিফ মহিউদ্দীনকে আটক করা হয়। দীর্ঘ কয়েকমাস কারাগারে আটকে রেখে তাদের জামিনে মুক্তি দেয়া হয়।
- রাইফ বাদাওয়ি নামের এক ব্লগারকে ধর্মের প্রতি ক্রিটিকাল একটি লিবারেল সৌদি ওযেব সাইট প্রতিষ্ঠা এবং লেখার দায়ে গ্রেফতার করা হয়। তাকে সাত বছরের জেল এবং ৬০০ চাবুকের বিধান দেয়া হয়েছে।
- ২০১৪ সালের মে মাসে নাইজেরিয়ার বোর্নো এলাকা থেকে ২২৩ জন স্কুলছাত্রীকে অপহরণ করে মুসলিম জঙ্গি দল বোকো হারাম। বিবৃতিতে তারা বলে, ‘মেয়েদের স্কুলে যাওয়া উচিৎ না। বরং তাদের বিয়ে দিয়ে দেয়া উচিৎ। আল্লাহ তাদেরকে বিক্রি করে দ্যোর নির্দেশ দিয়েছেন।
বলা নিষ্প্রয়োজন, উপরের লিস্টটি কেবল বিগত কয়েক শতকের কতিপয় ধর্মীয় সহিংসতার আলোকচ্ছটা মাত্র, সিন্ধুর বুকে বিন্দুসম। ধর্মীয় সহিংসতার পুরো ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে গেলে তা নিঃসন্দেহে মহাভারতকেও ছাড়িয়ে যাবে। অন্ধবিশ্বাস নামক ভাইরাসগুলো কীভাবে সন্ত্রাসবাদী তৈরির কারখানা হিসেবে ব্যবহৃত হয়-তার কিছু উদাহরণ আমরা আগেই রেখেছি এই বইয়ের পূর্ববর্তী ‘ধর্মীয় নৈতিকতা’ অধ্যায়ে। সেখানে আমরা দেখিয়েছিলাম, ধর্মগ্রন্থের ভালো ভালো বাণীগুলো থেকে ভালোমানুষ হওয়ার অনুপ্রেরণা পায় কেউ, আবার সন্ত্রাসবাদীরা একই ধর্মগ্রন্থের ভায়োলেন্ট ভার্সগুলো থেকে অনুপ্রেরণা পায় সন্ত্রাসী হওয়ার। সেজন্যই তো ধর্মগ্রন্থগুলো-একেকটি ট্রোজান হর্স-ছদ্মবেশী ভাইরাস! এজন্যই একই ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে কেউ ইহুদি নাসারাদের সাথে যুদ্ধ করার লক্ষ্যে বিন লাদেন’ হয়ে যায়, আবার কেউবা পরিণত হয় সুফি সাধকে। কী করে হলফ করে বলা যাবে যে ধর্মগ্রন্থ থেকে পাওয়া নিচের ভাইরাসরূপী আয়াতগুলো সত্যিই জিহাদি সৈনিকদের সন্ত্রাসবাদে উৎসাহিত করছে না? পবিত্র কোরআন থেকে উদ্ধৃত করা যাক–
তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে… (২ : ২২১৬)।
আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্ত্বা ব্যতীত অন্য কোনো বিষয়ের জিম্মাদার নন! আর আপনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন (৪ : ৪৪)।
হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না; তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ জালেমদেরকে পথ প্রদর্শন করেন না (৫ : ৫১)।
যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম তালাশ করে, কস্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (কোরআন ৩ : ৮৫)।
আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে। যায় (৮ : ৩৯)।
তোমরা যুদ্ধ করো আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তার রাসুল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিজিয়া প্রদান করে (৯ : ২৯)।
অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দান মারো, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত করো তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ করো, না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ লও।…. যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, আল্লাহ কখনোই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না(৪৭ : ৪)।
অতএব, তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে চলে আসে। অত: পর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে তাদেরকে পাকড়াও করো এবং যেখানে পাও হত্যা করো। তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী বানিও না (৪ : ৪৯)।
আর তাদেরকে হত্যা করো যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে … (২: ১৯১)
আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই করো, যে পর্যন্ত না। ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। (২: ১৯৩)।
আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব। কাজেই গর্দানের ওপর আঘাত হানো এবং তাদেরকে কাটো জোড়ায় জোড়ায় (৮ : ১২)।
অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা করো যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দি করো এবং অবরোধ করো। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁত পেতে বসে থাকো (৯ : ৫)।
যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আজাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন (৯ : ৩৯) …ইত্যাদি।
অনেক ইসলাম ধর্মবিশ্বাসীরা বলেন, কোরআন কখনও সন্ত্রাসবাদে কাউকে উৎসাহিত করে না, কাউকে আত্মঘাতী বোমা হামলায় প্ররোচিত করে না, ইত্যাদি। এটা সত্যি সরাসরি হয়ত কোরআনে বুকে পেটে বোমা বেধে কারো উপরে হামলে পড়ার কথা নেই; কিন্তু এটাও তো ঠিক যে, কোরআন খুললেই পাওয়া যায়-যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, আল্লাহ কখনোই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না (৪৭ : ৪), কোরআনে বলা হয়েছে আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনও মৃত মনে করো না (৩ : ১৬৯); কিংবা বলা। হয়েছে-যদি আল্লাহর পথে কেউ যুদ্ধ করে মারা যায় তবে তার জন্য রয়েছে জান্নাত (৯ : ১১১)।
আর আল্লাহর পথে শহীদদের জন্য জান্নাতের পুরস্কার কেমন হবে? আল্লাহ কিন্তু এ ব্যাপারে খুব পরিষ্কার তথায় থাকবে আনতন্যনা রমণীগণ, কোনো জিন ও মানব পূর্বে যাদের ব্যবহার করে নি (৫৫ : ৫৬)। তাদের কাছে থাকবে নত, আয়তলোচনা তরুণীগণ, যেন তারা সুরক্ষিত ডিম (৩৭ : ৪৮-৪৯); সুশুভ্র (wine) যা পানকারীদের জন্যে সুস্বাদু (৩৭ : ৪৬)।
আমি তাদেরকে আয়তলোচনা হুরদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দেব (৫২ : ২) …
তাবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ (৫৫ : ৭২); প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ (৫৫ : ৫৮)।
উদ্যান, আঙ্গুর, পূর্ণযৌবনা তরুণী এবং পূর্ণ পানপাত্র (৭৮ : ৩৩-৩৪)।
তথায় থাকবে আনতনয়না হুরিগণ, আবরণে রক্ষিত মোতির ন্যায়, (৫৬ : ২২-২৩)।
আমি জান্নাতি রমণীগণকে বিশেষরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তাদেরকে করেছি চিরকুমারী (৫৬ : ৩৫ ৩)।
শুধু আয়তলোচনা চিরকুমারীদের লোভ দেখিযেই আল্লাহ ক্ষান্ত হন নি, ব্যবস্থা রেখেছেন গেলমানদেরও—
সুরক্ষিত মোতিসদৃশ কিশোররা তাদের খেদমতে ঘোরাফেরা করবে (৫২ : ২৪)। ইত্যাদি।
বেহেস্তে সুরা-সাকি-হুর-পরীর এমন অফুরন্ত ভাণ্ডারের গ্রাফিক বর্ণনা দেখে দেখে অনেকেরই শহীদ হতে মন চাইবে! বিবর্তনবাদী মনোবিজ্ঞানী সাতোসি কানাজাওয়া তো মনেই করেন ইসলামি সমাজে বহুগামিত্ব এবং পাশাপাশি মৃত্যুর পরে উদ্ভিন্নযৌবনা এবং চিরকুমারী হুরিদের অফুরন্ত ভাণ্ডারের নিশ্চয়তার কারণেই মুসলিমদের মধ্যে আত্মঘাতী বোমা হামলাকারীদের এত আধিক্য চোখে পড়ে[৩১৫]।
কেবল ইসলামের জিহাদি সৈনিকেরাই ভাইরাস আক্রান্ত মননের উদাহরণ ভাবলে ভুল হবে। বিশ্বাসের ভাইরাস’ লেখাটি মুক্তমনায় প্রকাশের পর দিগন্ত সরকার ‘বিশ্বাসের ভাইরাস এবং আনুষঙ্গিক’ নামের একটি সম্পূরক প্রবন্ধে ভারতের আর. এস. এস পরিচালিত স্কুলগুলোর পাঠ্যসূচির নানা উদাহরণ হাজির করে দেখিয়েছেন কীভাবে ছেলেপিলেদের মধ্যে শৈশবেই ভাইরাসের বীজ বপন করা হয়[৩১৬]। বিদ্যাভারতী নামের এই স্কুল সারাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছে-সংখ্যায় প্রায় ২০,০০০। প্রায় ২৫ লাখ শিক্ষার্থী এতে পড়াশোনা করে-যাদের অধিকাংশই গরিব বা নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের। পড়াশোনা চলে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি অবধি। তিস্তা সেতালবাদের প্রবন্ধ In the Name of History Examples from Hindutva-inspired school textbooks in India থেকে[৩১৭] অসংখ্য দৃষ্টান্ত হাজির করে দিগন্ত দেখিয়েছেন কীভাবে সত্য মিথ্যের মিশেল দেওয়া ইতিহাস পড়িযে এদের মগজ ধোলাই করা হয়–
‘‘হোমার বাল্মীকির রামায়ণের একটা ভাবানুবাদ করেছিলেন-যার নাম ইলিয়াডা’ ‘প্লেটো ও হেরোডোটাসের মতে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা ভারতীয় ভাবধারার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল।
‘গরু আমাদের সকলের মাতৃস্থানীয়, গরুর শরীরে ভগবান বিরাজ করেন।
একই স্কুলের ভারতের ম্যাপে ভারতকে দেখানো হয় বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, তিব্বত এমনকি মায়ানমারের কিছু অংশ নিয়ে বলা হয় অশোকের অহিংস নীতির ফলে তার সেনাবাহিনী যুদ্ধে উৎসাহ হারিয়েছিল। আলেকজান্ডার নাকি পুরুর কাছে যুদ্ধে হেরে গিযে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছিলেন।
মধ্যযুগের ইতিহাসে সাম্প্রদায়িকতার উগ্ররূপ আর বেশি প্রকট। সমগ্র ইতিহাস শিক্ষায় মুসলিমদের বিদেশি শক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছেঃ
‘ভারতে বিদেশি মুসলিম শাসন
‘ভারতে তলোয়ার ধরে ইসলামের প্রচার হয়েছিল। মুসলিমেরা এক হাতে কোরআন আরেক হাতে তরবারি নিয়েই এসেছিল এদেশে … আমরা তাদের পরে তাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি, কিন্তু আমাদের যে ভাইযেরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তাদের হিন্দুধর্মে ধর্মান্তরিত করতে ব্যর্থ হয়েছি।”
‘হিন্দুরা চরম অপমানের সাথে তুর্কি শাসন মেনে নিয়েছিল।
‘বাল্যবিবাহ, সতীদাহ, পর্দাপ্রথাসহ আরও অনেক কুসংস্কার মুসলিম রাজত্বের প্রতিক্রিয়া হিসেবে হিন্দুসমাজে স্থান করে নিয়েছে’
‘শিবাজী আর রানা প্রতাপ ছিলেন প্রকৃত স্বাধীনতা সংগ্রামী। তারা মুসলিমদের দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্যই লড়াই করেছিলেন।’’
ভারতের স্কুলের পাঠ্য পুস্তকগুলোতে বিন কাশিম, ঘৌরী বা গজনীর মাহমুদ বা তৈমুর লং কীভাবে হিন্দুদের হত্যা করেছিলেন তার বিস্তারিত বর্ণনা হাজির করে বাচ্চাদের মাথায় অঙ্কুরেই ‘মুসলিম বিদ্বেষ প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। দেশ বিভাগের জন্য একতরফাভাবে মুসলিমদের দায়ী করে ইতিহাস লেখা হয়। আর. এস. এস-এর মতো সন্ত্রাসবাদী সাম্প্রদায়িক দলকে প্রকৃত স্বাধীনতাকামী একটি সংগঠন হিসেবে তুলে ধরা হয়। সব থেকে মজার কথা, মহাত্মা গান্ধী যে এই সংগঠনের একজনের হাতেই মারা গিয়েছিলেন, সেকথাও বেমালুম চেপে যাওয়া হয়। সামগ্রিকভাবে, পাঠক্রম এমনভাবে সাজানো যাতে সবার মধ্যে ভাব সৃষ্টি হয় যে তাদের পূর্বপুরুষেরা মুসলিম ও খ্রিস্টানদের হাতে অত্যাচারিত। তাদের ঘাড়ে দায়িত্ব বর্তায় তার প্রতিশোধ নেওয়ার।
২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর সেইদিন প্রায় ৫০ জন জঙ্গি মুম্বাইয়ের তাজ হোটেলে সন্ত্রাসবাদের যে তুঘলকি কাণ্ড শুরু করেছিল সেদিন এই বিশ্বাসের ভাইরাস নিয়ে আমরা মুক্তমনায় দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল। বিশ্বাসের বাইরেও রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ইস্যুসহ নানা ধরনের আকর্ষণীয় প্রসঙ্গ উঠে এসেছিল বিস্তৃত পরিসরে উঠে এসেছিল কাশ্মীর প্রসঙ্গ, উঠে এসেছিল ভারতে মুসলিম জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যের নানা উদাহরণ। এটা ঠিক যে, কাশ্মীরী জনগণের ওপর ভারতীয় সেনাবাহিনীর লাগাতার অত্যাচার, বাবরি মসজিদ ধ্বংস কিংবা গুজরাটে সাম্প্রতিক সময়ে মুসলিমদের ওপর যে ধরনের অত্যাচারের স্টিমরোলার চালানো হয়েছে তা ভুলে যাওয়ার মতো বিষয় নয়। মুসলিমরা ভারতের জনগণের প্রায় ১৪ শতাংশ। অথচ তারাই ভারতে সবচেয়ে নিপীড়িত, অত্যাচারিত এবং আর্থসামাজিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া এক জনগোষ্ঠী। এ সমস্ত অনেক কারণ মুসলিমদের ক্ষুব্ধ করেছে বছরের পর বছর ধরে। কিন্তু এটাও ঠিক, পৃথিবীতে সামাজিক অবিচার যেমন আছে, তেমন আছে সামাজিক অবিচারের নামে অন্ধবিশ্বাসের চাষ এবং তার প্রচার। ধর্মগ্রন্থের জিহাদি বাণীগুলো কিংবা সুচতুর উপায়ে বিকৃত ইতিহাস তুলে ধরে পরবর্তী প্রজন্মকে মগজ ধোলাইযের উদাহরণগুলো এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মুক্তমনা সদস্য অপার্থিব জামান আমাদের সাইটে প্রবন্ধটি নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে যা বলেছেন তা হয়ত অনেকের মনেই চিন্তার খোরাক জোগাবে। তিনি বলেন–
মানুষের কোনো কোনো স্বভাব যেমন উপযুক্ত পরিবেশ পাওয়ায় বিশেষ কোনো বংশাণুর পরিস্ফুটনের কারণে সৃষ্ট হয়, তেমনই মৌলবাদী সন্ত্রাসও ঘটতে পারে কোনো কোনো ধর্মীয় আদেশাবলীর উপযুক্ত পরিবেশ পাওয়ায় পরিস্ফুটিত হওয়ার কারণে। এই উপযুক্ত পরিবেশ প্রদান করতে পারে অনেক কারণ, যার মধ্যে সামাজিক অনাচার অবশ্যই অন্যতম। কিন্তু শুধু সামাজিক অনাচার থাকলেই যে মৌলবাদী সন্ত্রাস ঘটবে এটা নিশ্চিত না। বংশাণুর মতো একটা মূল কারণও থাকতে হবে (মৌলবাদী সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে যা হতে ধর্মগ্রন্থের কোনো কোনো শ্লোক, কিংবা জাতিবিদ্বেষী বিকৃত ইতিহাস চর্চা)। আর এই ধর্মীয় বংশাণু কেবল সামাজিক অনাচারেই পরিস্ফুটিত হয়-তাও হলফ করে বলা যাবে না। কোনো কোনো ধর্মের আদেশাবলী এতই শক্তিশালী যে বিভিন্ন পরিস্ফুটক পরিবেশ অতি সহজেই সৃষ্ট হয় আদেশাবলীর জোরালো তাগিদেই। আর ধর্মীয় মূল কারণ না থাকলে সামাজিক অনাচার অন্যরকম সন্ত্রাসের জন্ম দিতে পারে। আবার নাও দিতে পারে।
থাইল্যান্ডে অতি গরিব বৌদ্ধরা ভিক্ষা করবে কিন্তু কখনও হিংসায় লিপ্ত হবে না। অনেক গরিব লোক চরম দারিদ্রের মধ্যেও সততা বিসর্জন দেয় না। তিব্বতিদের ওপর অত্যাচার হয়েছে অনেক বেশি। কিন্তু তিব্বতের লোকেরা হিংসার আশ্রয় নিয়ে সন্ত্রাসবাদী হয় নি। কাজেই এটা কখনোই বলা যায় না যে সামাজিক অনাচারই ধর্মীয় সন্ত্রাসের মূল কারণ, বরং বলা যায় অনুঘটক মাত্রা।
.
বিশ্বাস এবং বুদ্ধিমত্তা
বহুদিন ধরেই এ ব্যাপারটা প্রচলিত যে, অবিশ্বাসীরা সাধারণত বিশ্বাসীদের চেয়ে অধিকতর বুদ্ধিদীপ্ত এবং স্মার্ট হয়ে থাকে। সম্প্রতি বিভিন্ন বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানীদের চালানো জরিপে চাঞ্চল্যকর কিছু ফল এবং ব্যাখ্যা উঠে এসেছে।
লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিকসের বিবর্তন মনোবিজ্ঞানী সাতোসি কানাজাওযার চালানো সাম্প্রতিক গবেষণা (Social Psychology Quarterly, Vol. 73, No. 1, 33–57) থেকে জানা গেছে নাস্তিক (Atheist) এবং উদারপন্থীরা (Liberal) সাধারণত ধার্মিক (Theist) এবং রক্ষণশীলদের (Conservative) চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে থাকে। সোশাল সাইকোলজি কোয়ার্টারলি জার্নালে ২০১০ সালে প্রকাশিত ‘Why Liberals and Atheists Are More Intelligent শীর্ষক গবেষণাপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ধার্মিক হিসেবে দাবিদার ব্যক্তিদের চেয়ে নাস্তিকদের আইকিউ গড়পড়তা অন্তত ৬ পয়েন্ট বেশি থাকে, আর রক্ষণশীল গ্রুপের চেয়ে উদারপন্থী বা প্রগতিশীল গ্রুপের আইকিউ বেশি থাকে অন্তত ১২ পয়েন্ট[৩১৮]।
ছবি। পেজ ৩৯০
চিত্র : ধার্মিকতার প্রকোপ যত বাড়ে পাল্লা দিয়ে কমে আইকিউ। যেমন চরম নাস্তিকদের গড়পড়তা আইকিউ পাওয়া গেছে ১০৩.০৯ আর চরম ধার্মিকদের আইকিউ ৯৭.১৪। কাজেই নাস্তিক হিসেবে দাবিদার ব্যক্তিদের চেয়ে আস্তিকদের আইকিউ গড়পড়তা অন্তত ৬ পয়েন্ট কম থাকে।
ছবি। পেজ ৩৯১
চিত্র : রক্ষণশীল গ্রুপের চেয়ে উদারপন্থী বা প্রগতিশীল গ্রুপের আইকিউ অন্তত ১২ পয়েন্ট বেশি থাকে।
ব্যাপারটি অধ্যাপক কানাজাও বিবর্তনীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন তার প্রকাশিত গবেষণাপত্রে এবং ব্লগে[৩১৯,৩২০]। তিনি তার ব্যাখ্যায় বলেছেন, বিশ্বাস ব্যাপারটা একসময় টিকে থাকার ক্ষেত্রে বড় নিয়ামক হিসেবে কাজ করেছিল, সেজন্য যেকোনো সংস্কৃতিতেই ধর্ম এবং বিশ্বাসের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়, এবং যেকোনো সমাজেই ধার্মিকদের সংখ্যাও নাস্তিকদের চেয়ে সাধারণত বেশি (যদিও নাস্তিকদের সংখ্যা আধুনিক বিশ্বে ক্রমবর্ধমান)। আর আদিম ট্রাইবগুলোতে খুঁজলে দেখা যাবে সেখানে জাদুটোনা থেকে শুরু করে নরবলি, কুমারী নিধনসহ হাজারো অপবিশ্বাসের সমাহার। সে দিক থেকে চিন্তা করলে নাস্তিকতা, যুক্তিবাদ, বিজ্ঞানমনস্কতা, লিবারেলিজম প্রভৃতি উপাদানগুলো বিবর্তনীয় প্রেক্ষাপটে মানবসমাজের জন্য অপেক্ষাকৃত নতুন সংযোজন (evolutionarily novel) এবং যাদের মস্তিষ্ক এই নতুন নতুন পরিবর্তনগুলো ধারণ করার জন্য বেশি নমনীয়, তারাই বুদ্ধিদীপ্ত হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। সেজন্যই নাস্তিকেরা আস্তিকদের থেকে বেশি স্মার্ট হিসেবে আবির্ভূত হয়, বিবর্তনীয় মনোবিজ্ঞানের ‘সাভানা অনুকল্প অনুযায়ী এটা ঘটে বলে গবেষণাপত্রে দাবি করা হয়েছে। সেজন্যই একজন বিশ্বাসী সারা প্যালিন কিংবা উইচ’ খ্যাত ক্রিস্টিন ওডেনেলের চেয়ে বৌদ্ধিক মননে একজন রিচার্ড ডকিন্স কিংবা একজন বিল মার অনেক এগিয়ে থাকেন আজকের দুনিয়ায়। সদালাপী’দের চেয়ে যুক্তিতে, বুদ্ধিতে আর সাংস্কৃতিকভাবে অগ্রগামী থাকেন ‘মুক্তমনারা। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ফলাফলটি এসেছে ইউসিএসডি এবং হার্ভার্ডের সাম্প্রতিক একটা যৌথ গবেষণা থেকে যেখানে ডোপামিন নির্ভর DRD, জিনটিকে চিহ্নিত করা গেছে বলে দাবি করা হয়েছে, এবং যার একটা বিশেষ ভ্যারিযান্ট উদারপন্থীদের মাঝে দেখা যায়[৩২১]। এ জিনটিকে বহুল প্রচারিতভাবে ‘অভিনবত্ব অনুসন্ধানী জিন (novelty seeking gene) হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। যাদের মধ্যে এ জিনটির অস্তিত্ব আছে, তার একটা বড় অংশ পরিণত বয়সে উদারপন্থী মতাদর্শের সাথে যুক্ত হয়ে পড়েন বলে গবেষণায় উঠে এসেছে।
এ ব্যাপারে একটা মজার বিষয় মনে পড়ল। আমেরিকার প্রচণ্ড রক্ষণশীল ফক্স চ্যানেলের নিউজ হোস্ট শন হ্যানিটি আর বিল ও রাইলি প্রতিদিনই মার্কিন জনগণকে মনে করিয়ে দেন যে কীভাবে লিবারেল মিডি’ সবকিছু অধিকার করে মগজ ধোলাই করছে! কথাটা যে খুব বেশি মিথ্যা তা অবশ্য নয়। হলিউড সিনেমা থেকে শুরু করে (ফক্স বাদে) প্রায় প্রতিটি নিউজ চ্যানেলই মোটামুটি লিবারেলদের দখলে বলা যায়।
পাশাপাশি শো বিজনেস, ক্রিযেটিভ রাইটিং, অ্যাক্টিভিজম থেকে শুরু করে অ্যাকাডেমিয়াও মোটামুটি লিবারেলরাই রাজত্ব করছে। আসলে এর কারণ খুব সহজ। মিডিয়া লিবারেলদের হাতে চলে যাচ্ছে কারণ রক্ষণশীলদের চেয়ে তারা বেশি বুদ্ধিমান, চৌকস, বুদ্ধিদীপ্ত এবং অধিকতর বেশি উদ্ভাবনী শক্তির অধিকারী। বাংলাদেশেও কবি সাহিত্যিকসহ যারা শিল্পকলা এবং সংস্কৃতির সাথে জড়িত থাকেন তাদের মধ্যে উদারপন্থী লোকের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে, এবং তাদের মধ্যেই অবিশ্বাসীদের সংখ্যা বেশি পাওয়া যায়।
ছবি। পেজ ৩৯৩
ছবি। পেজ ৩৯৪
চিত্র : একজন প্রথাগত বিশ্বাসীর চেয়ে অনেক এগিয়ে থাকেন একজন সচেতন নাস্তিক বৌদ্ধিক মনন, যুক্তি, বাস্তবতা এবং স্মার্টনেসে।
অবিশ্বাসীরা শুধু স্মার্ট নয়, গবেষণায় দেখা গেছে নৈতিক দিক দিয়েও অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের চেয়ে অনেক অগ্রগামী। নাস্তিক এবং প্রগতিশীল পরিবারে শিশু নির্যাতন কম হয়, তারা নারী নির্যাতন কম করে থাকে, তাদের পরিবারে বিবাহ বিচ্ছেদের হার কম, তারা একগামী সম্পর্কে আস্থাশীল থাকে, তারা পরিবেশ সচেতন থাকে ধার্মিকদের চেয়ে ঢের বেশি। সংখ্যালঘুদের প্রতি সহিষ্ণুতা এবং সংখ্যালঘুদের অধিকারের প্রতি সচেতনতাও বিশ্বাসীদের তুলনায় নাস্তিকদের মধ্যে অনেক বেশি দেখা যায়। এর কারণ, অবিশ্বাসীরা সাধারণত যুক্তি, মানবতা এবং বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বিষয়গুলো বিবেচনা করেন, অন্ধবিশ্বাসের বলে নয়।
.
বিশ্বাস ও দারিদ্র্য
বিশ্বাস শুধু মানসিকভাবেই ব্যক্তিকে পঙ্গু এবং ভাইরাস আক্রান্ত করে ফেলে না, পাশাপাশি এর সার্বিক প্রভাব পড়ে একটি দেশের অর্থনীতিতেও। সাম্প্রতিক বহু গবেষণায়ই বেরিয়ে এসেছে যে দারিদ্রের সাথে ধর্মবিশ্বাসের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। সম্প্রতি প্রকাশিত (অগাস্ট, ২০১০) গ্যালোপ জরিপ থেকে দেখা গেছে পৃথিবীর সবচেয়ে হতদরিদ্র দেশগুলোর মধ্যেই ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাব সর্বাধিক[৩২২]। আপনার বিশ্বাস প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় কোনো প্রভাব ফেলে কিনা, এর ভিত্তিতে ২০০৯ সালে যে জরিপ চালানো হয়, তাতে দেখা যায়। পৃথিবীর সর্বাধিক দারিদ্রকিষ্ট দেশগুলো থেকেই ‘হ্যাঁ বাচক উত্তর উঠে এসেছে। আর তালিকাতে প্রথমেই আছে বাংলাদেশের নাম।
Is religion an important part of your daily life?
Bangladesh —Yes –99%+
Niger ——– ,, –99%+
Yemen——– ,, –99%
Indonesia—– ,, –99%
Malawi——- ,, –99%
Sri Lanka——,, –99%
Somaliland region— ,, –98%
Djibouti —— ,, –98%
Mauritania— ,, –98%
Burundi —– ,, –98%
2009 GALLUP
গ্যালোপ জরিপ থেকে দেখা গেছে। পৃথিবীর সবচেয়ে হতদরিদ্র দেশগুলোর মধ্যেই ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রভাব সর্বাধিক।
সম্প্রতি উপরের এই গ্যালোপ জরিপের ওপর ভিত্তি করে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় বিশ্লেষণমূলক একটি সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে[৩২৩]। কলামিস্ট চার্লস ব্লো সম্পাদকীয়টিতে বলেন–
একশটি দেশের মধ্যে ২০০৯ সালে গ্যালোপ জরিপ। চালানো হয়েছে এবং দেখা গেছে দারিদ্রের সাথে ধর্মবিশ্বাসের একটি প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে। ধনী দেশগুলো কম ধর্মপ্রবণ আর দরিদ্র দেশগুলোতেই ধর্মান্মোদনা বেশি দৃশ্যমান।
নিউইয়র্ক টাইমসের উক্ত প্রবন্ধটিতে চমৎকার একটি গ্রাফও সংযুক্ত হয়েছে, যেটি নিজেই দারিদ্রের সাথে ধর্মবিশ্বাসের সম্পর্ককে ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট–
ছবি। পেজ ৩৯৭
চিত্র : গ্যালোপ জরিপের ওপর ভিত্তি করে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় বিশ্লেষণমূলক একটি সম্পাদকীয়তে প্রকাশিত।
উপরের গ্রাফের গড়পড়তা পয়েন্টগুলোর ট্রেন্ড বিশ্লেষণে আনা যেতে পারে। যদি কেউ কোনো দেশের ধর্মীয় প্রভাব এবং পার ক্যাপিটা গ্রস ডোমেস্টিক প্রডাক্টের প্লট একটি বক্ররেখার মাধ্যমে তুলে ধরেন তবে রেখচিত্রটি দাঁড়াবে অনেকটা এরকম–
ছবি। পেজ ৩৯৮
চিত্র : দেশের ধর্মীয় প্রভাব বনাম পার ক্যাপিটা জিডিপির প্লট
এই গ্রাফটি নিয়ে আমরা মুক্তমনা ব্লগে অনেক আলোচনা করেছি। এটি অধ্যাপক ভিক্টর স্টেরের ‘নিউ এথিজম’ বইয়ে আছে। ইন্টারনেটেও অনেক সাইটে গ্রাফটি পাওয়া যাবে[৩২৪]।
গ্রাফটি লক্ষ্য করলেই পাঠকেরা দেখবেন যে, আমেরিকা এবং কুয়েতের মতো দুযেকটি দেশ ছাড়া বাকি সব কমবেশি দেশই এই গ্রাফের কোরিলেশন সমর্থন করে। আমেরিকা অন্যতম সচ্ছল দেশ (গড় জিডিপি $৪৬,০০০) হওয়া সত্ত্বেও ধর্মের প্রভাব বেশি। ধনসম্পদে শীর্ষস্থানীয় দেশ হওয়া সত্বেও দেশটির ধর্মীয় প্রভাবের পরিমাপ দারিদ্রক্লিষ্ট মেক্সিকো, আর্জেন্টিনা কিংবা চিলির সারিতে রয়ে গেছে। কেন এই ব্যতিক্রম তা ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। একটি কারণ তো অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদী চেতনার বিকাশ। একটি দেশ যখন ক্ষমতার শীর্ষে উঠে যায়, সামরিকভাবে আগ্রাসী হয়ে উঠে, তখন আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কারণে প্রগতিশীল বৈশিষ্ট্যগুলো হারাতে থাকে। গ্রিক এবং রোমান সভ্যতার শেষদিকেও একই ব্যাপার ঘটেছিল। এর বাইরে, আরেকটি বড় কারণ, আমেরিকার পুঁজিবাদ ধর্ম জিনিসটাকেও আভ্যন্তরীণভাবে ব্যবসা’র পর্যায়ে নিয়ে যেতে পেরেছে। এখানে চার্চকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত উৎসবের আয়োজন করা হয়, তা আসলে ধর্মীয় পরিবৃত্তির বাইরে গিযেও সাধারণ জনগণকে আকৃষ্ট করে। সাধারণ বসন্ত উৎসব (ফল ফেস্টিভাল) থেকে শুরু করে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের ক্লাসিক্যাল পিয়ানো বাজনার বেশিরভাগই এখানে চর্চাকেন্দ্রিক। এই ‘আমেরিকান অ্যানোমালি’ আর অস্বাভাবিক উপায়ে অর্জিত তেল সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের কথা বাদ দিলে ধর্ম এবং দারিদ্র্যের একটা স্পষ্ট সম্পর্কই পাওয়া যায়। নবায়নযোগ্য শক্তির বিকাশ এবং এ সংক্রান্ত প্রযুক্তির উত্থানের ফলে ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে তেলের দাম পড়ে গেলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোও এভাবে ব্যতিক্রম হিসেবে থাকবে না বলাই বাহুল্য।
এই দুই একটি অ্যানোমালি তথা ‘অস্বাভাবিকতা বাদ দিলে গ্রাফ থেকে ধর্ম এবং দারিদ্র্যের একটা স্পষ্ট সম্পর্কই পাওয়া যায়। গ্রাফ দেখলে যে কেউ বুঝবে যে দেশে ধর্মীয় প্রভাব যত বাড়ছে, সেইসাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দারিদ্র আর ধর্মীয় প্রভাব যেখানে কম মানুষের সচ্ছলতাও বেশি। ব্যাপার কী?
ব্যাপার তো সাদা চোখেই বোঝা যাওয়ার কথা। যে সমস্ত দেশ যত দারিদ্রক্লিষ্ট, সেসব দেশেই ধর্ম নিয়ে বেশি নাচানাচি হয়, আর শাসকেরাও সেসব দেশে ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। সেজন্যই দারিদ্রক্লিষ্ট দেশগুলোতে ধর্ম খুব বড় একটা নিয়ামক হয়ে কাজ করে সবসময়েই। কিংবা ব্যাপারটা উল্টোভাবেও দেখা যেতে পারে ধর্মকে অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেওয়া, কিংবা লম্ফঝম্ফ করা, কিংবা জাগতিক বিষয়আশয়ের চেয়ে ধর্মকে মাত্রাতিরিক্ত বেশি গুরুত্ব দেওয়ার কারণেই সেসমস্ত দেশগুলো প্রযুক্তি, জ্ঞান বিজ্ঞানে পিছিয়ে এবং সর্বোপরি দরিদ্র কিছুদিন আগে বাংলাদেশ সরকার মোল্লাদের তোয়াজ করতে ফেসবুক বন্ধ করে দিয়েছিল। যে দেশ জাগতিক বিষয়ের চেয়ে ঠুনকো বিশ্বাস নিয়েই মত্ত থাকে, সে দেশ অর্থ-বৈভব জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নত হয়ে যাবে-এটা কি আশা করা যায়? ধর্মের রশি আমাদের পেছনে টেনে রেখেছে অনেকটাই। বিশ্বাসের ভাইরাসের এরচেয়ে বড় কুফল আর কী হতে পারে! তাই বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর’ বলে কথিত বিশ্বাসীদের তোতা পাখির মতো আওড়ানো বহুল প্রচারিত উক্তিটিকে সামান্য বদলে দিয়ে আমরা বলতে পারি–
বিশ্বাসে মিলায় দারিদ্র্য, অবিশ্বাসে বহুদূর!
.
ভাইরাস প্রতিষেধক
তাহলে এই সন্ত্রাসের ভাইরাস প্রতিরোধ করা যায় কী করে? ভাইরাস যে প্রতিরোধ করতেই হবে-এ নিয়ে কারো সন্দেহ থাকার কথা নয়। এ ভাইরাস প্রতিরোধ না করতে পারলে এ সভ্যতার ক্যান্সারে রূপ নিয়ে আমাদের সমস্ত অর্জনকে ধ্বংস করবে। মুম্বাইয়ে ফিদাইন হানার পর পরই মুক্তমনায় লিখিত একটিপ্রবন্ধে ড. বিপ্লব পাল বলেছিলেন[৩২৫]–
রাষ্ট্র, পরিবার, সমাজ ইত্যাদির ধারণাগুলোর বৈপ্লবিক পরিবর্তন হচ্ছে-তখন মধ্যযুগীয় ধর্মগুলোর আত্মিক উন্নতির কিছু বাণী ছাড়া আর কিছুই আমাদের দেওয়ার নেই। সেই আত্মিক উন্নতির নিদান ধর্ম ছাড়াও বিজ্ঞান থেকেই পাওয়া যায়-তবুও কেউ আত্মিক উন্নতির জন্য ধার্মিক হলে আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু ধর্মপালন যখন তার হিন্দু বা মুসলমান পরিচয়বোধকে উস্কে দিচ্ছে-সেটা খুব ভয়ংকর। ধর্ম থেকে সেই বিষটাকে আলাদা করতে না পারলে, এগুলো আমাদের সভ্যতার ক্যান্সার হয়ে আমাদের সমস্ত অর্জনকে ধ্বংস করবে।
অর্থাৎ, এ ভাইরাসকে না থামিয়ে বাড়তে দিলে একসময় সারা দেহটাকেই সে গ্রাস করে ফেলবে। অধ্যায়ের প্রথম দিকে দেওয়া ল্যাংসেট ক্লক প্যারাসাইট আক্রান্ত পিঁপড়ার উদাহরণের মতো মানবজাতিও একসময় করে তুলবে নিজেদের আত্মঘাতী, মড়ক লেগে যাবে পুরো সমাজে। তাই কি আমরা চাই?
না, কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষই তা চাইতে পারেন। তাহলে এই সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কী? এই ভাইরাস সংক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য গড়ে তোলা দরকার অ্যান্টিবডি, সহজ কথায় তৈরি করা দরকার ভাইরাস প্রতিষেধকের। আর এই সাংস্কৃতিক ভাইরাসকে প্রতিরোধ করতে পারে আমার আপনার মতো বিবেকসম্পন্ন প্রগতিশীল মানুষেরাই। আমরা কিন্তু আসলেই মনে করি-এই অ্যান্টিবডি তৈরি করতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে আমাদের মুক্তমনার মতো বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী সাইটগুলো; ভূমিকা রাখতে পারে বিশ্বাসের নিগড় থেকে বেরুনো মানবতাবাদী গ্রুপগুলো এবং মুক্তবুদ্ধির চর্চাকারী ব্যক্তিবর্গ 26। দরকার সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টার, দরকার খোলস ছেড়ে বেরুনোর মতো সৎ সাহসের, দরকার আমার-আপনার সকলের সামগ্রিক সদিচ্ছার। আপনার আমার এবং সকলের আলোকিত প্রচেষ্টাতেই হয়ত আমরা একদিন সক্ষম হব সমস্ত বিশ্বাসনির্ভর ‘প্যারাসাইটিক’ ধ্যান ধারণাগুলোকে তাড়াতে, এগিযে যেতে সক্ষম হব বিশ্বাসের ভাইরাসমুক্ত নিরোগ সমাজের অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে।
ড. ড্যারেল রে যে কথাগুলো বলে তার গড় ভাইরাস’ বইটি শেষ করেছেন[৩২৭],সে কথাগুলো উচ্চারণ করে আমরাও সমাপ্তি টানবো এই অধ্যায়টির–
ভাইরাসমুক্ত জীবনের আস্বাদন কোনো সুনির্দিষ্ট গন্তব্য নয়, বরং একটি চলমান যাত্রাপথের নাম। আমরা সবাই এই ভাইরাস দিয়ে কোনো না কোনোভাবে আক্রান্ত এবং আমরা নিজেদের অজান্তেই বয়ে নিয়ে যাই অসুস্থ বিশ্বাস, মতামত কিংবা ধারণা। শিশু বয়সেই ধর্মীয় বিশ্বাসের পানপাত্র হাতে তুলে দিয়ে আমাদের অনেকের মাথাই আক্রান্ত করে ফেলা হয়েছে। আক্রান্ত মননকে প্রতিষেধক দিয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ করে ফেলাই হবে আমাদের যাত্রাপথের লক্ষ্য। আমরা যদি ঈশ্বর-ভাইরাসের কুফলগুলো সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকতে পারি, তবেই আমরা ভাইরাসমুক্ত সমাজ প্রত্যাশা করতে পারি।
আমাদের ধারণা, নতুন দিনের নাস্তিকেরাই ভাইরাস মুক্ত সমাজ নির্মাণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে ভবিষ্যতের পৃথিবীতে। আর নতুন দিনের নাস্তিকদের ক্রমিক প্রচেষ্টার কিছু নিদর্শন তুলে ধরা হবে পরের অধ্যায়ে।
০৯. নতুন দিনের নাস্তিকতা : আগামী দিনের ভাইরাস-মুক্ত সমাজ
ঈশ্বর খুবই ভঙ্গুর; বিজ্ঞানের ছোট্ট একটি ফুলকি অথবা একটু সাধারণ জ্ঞানই তাকে মেরে ফেলতে সক্ষম। –চ্যাপম্যান কোযেন
বিশ্বাসের দীনতা
১৬৩৩ সাল। পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে-বাইবেল বিরোধী এই সত্য কথা বলার অপরাধে চার্চ খ্যাতনামা বিজ্ঞানী গ্যালিলিওকে অভিযুক্ত করল ‘ধর্মদ্রোহিতা’র অভিযোগে। গ্যালিলিও তখন প্রায় অন্ধ, বয়সের ভারে ন্যুজ। অসুস্থ ও বৃদ্ধ বিজ্ঞানীকে জোর করে ফ্লোরেন্স থেকে রোমে নিয়ে যাওয়া হলো, হাঁটু ভেঙে সবার সামনে জেড হাতে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়ে বলতে বাধ্য করা হয় এতদিন গ্যালিলিও যা প্রচার করেছিলেন তা ধর্মবিরোধী, ভুল ও মিথ্যা। বাইবেলে যা বলা হয়েছে সেটিই আসল, সঠিক-পৃথিবী স্থির অনড় সৌর জগতের কেন্দ্রে[৩২৮]। গ্যালিলিও প্রাণ বাঁচাতে তাই করলেন। পোপ ও ধর্মসংস্থার সম্মুখে গ্যালিলিও যে স্বীকারোক্তি ও প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করেন, তা বিজ্ঞান সাধনার ইতিহাসে ধর্মীয় মৌলবাদীদের নির্মমতার এবং জ্ঞান সাধকদের কাছে বেদনার এক ঐতিহাসিক দলিল[৩২৯]–
আমি ফ্লোরেন্সবাসী স্বর্গীয় ভিন্সেঞ্জিও গ্যালিলিওর পুত্র, সত্তর বৎসর বয়স্ক গ্যালিলিও গ্যালিলি সশরীরে বিচারার্থ আনীত হয়ে এবং অতি প্রখ্যাত ও সম্মানার্য ধর্মযাজকদের (কার্ডিনাল) ও নিখিল খ্রিস্টীয় সাধারণতন্ত্রে ধর্মবিরুদ্ধ আচরণজনিত অপরাধের সাধারণ বিচারপতিগণের সম্মুখে নতজানু হয়ে স্বহস্তে ধর্মগ্রন্থ স্পর্শ-পর্বক শপথ করছি যে, রোমের পবিত্র ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্ম সংস্থার দ্বারা যা কিছু শিক্ষাদান ও প্রচার করা হয়েছে ও যা কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করা হয়েছে আমি তা সবসময় বিশ্বাস করে এসেছি, এখনও করি এবং ঈশ্বরের সহায়তা পেলে ভবিষ্যতেও করব। সূর্য কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত ও নিশ্চল এরূপ মিথ্যা অভিমত যে কীরূপ শাস্ত্রবিরোধী সেসব বিষয় আমাকে অবহিত করা হয়েছিল; এ মিথ্যা মতবাদ সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে এর সমর্থন ও শিক্ষাদান থেকে সর্বপ্রকারে নিবৃত্ত থাকতে আমি এই পবিত্র ধর্মসংস্থা কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলাম। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সে একই নিন্দিত ও পরিত্যক্ত মতবাদ আলোচনা করে ও কোনো সমাধানের চেষ্টার পরিবর্তে সেই মতবাদের সমর্থনে জোরালো যুক্তিতর্কের অবতারণা করে আমি একটি গ্রন্থ রচনা করেছি। এজন্য গভীর সন্দেহ এই যে আমি খ্রিস্টধর্মবিরুদ্ধ মত পোষণ করে থাকি। ….
অতএব সঙ্গত কারণে আমার প্রতি আরোপিত এই অতিঘোর সন্দেহ ধর্মাবতারদের ও ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেকের মন হতে দূর করার উদ্দেশ্যে সরল অন্তঃকরণে ও অকপট বিশ্বাসে শপথ করে বলছি যে পূর্বোক্ত ভ্রান্ত ও ধর্মবিরুদ্ধ মত আমি ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করি। …আমি শপথ করে বলছি যে, আমার উপর এ জাতীয় সন্দেহের উদ্রেক হতে পারে, এরূপ কোনো বিষয় সম্বন্ধে ভবিষ্যতে আর কখনও কিছু বলব না বা লিখব না এরূপ অবিশ্বাসীর কথা জানতে পারলে অথবা কারও ওপর ধর্মবিরুদ্ধ মতবাদ পোষণের সন্দেহ উপস্থিত হলে পবিত্র ধর্মসংস্থার নিকট অথবা যেখানে অবস্থান করব সেখানকার বিচারকের নিকট আমি তা জ্ঞাপন করব। শপথ নিয়ে আমি আরও প্রতিজ্ঞা করছি যে, এই পবিত্র ধর্মসংস্থা আমার ওপর যেসব প্রায়শ্চিত্তের নির্দেশ প্রদান করবে আমি তা হুবহু পালন করব। এসব প্রতিজ্ঞা ও শপথের যেকোনো একটি যদি ভঙ্গ করি তাহলে শপথভঙ্গকারীর জন্য ধর্মাধিকরণের পবিত্র অনুশাসনে এবং সাধারণ অথবা বিশেষ আইনে যেসব নির্যাতন ও শাস্তির ব্যবস্থা আছে তা আমি মাথা পেতে গ্রহণ করব। অতএব ঈশ্বর ও যেসব পবিত্র গ্রন্থ আমি স্পর্শ করে আছি এরা আমার সহায় হোন। আমি উপরে কথিত গ্যালিলিও গ্যালিলি শপথ গ্রহণ ও প্রতিজ্ঞা করলাম এবং নিজেকে উপযুক্তভাবে বন্ধনে আবদ্ধ রাখতে প্রতিশ্রুত হলাম। এর সাক্ষ্য হিসেবে স্বহস্তলিখিত শপথনামা যার প্রতিটি অক্ষর এইমাত্র আপনাদের পাঠ করে শুনিয়েছি তা আপনাদের নিকট সমর্পণ করছি। (২২শে জুন, ১৬৩৩ খ্রিস্টাব্দ, রোমের মিনার্ভা কনভেন্ট)।
শোনা যায়, এর মধ্যেও একবার আকাশের দিকে তাকিযে বৃদ্ধ গণিতজ্ঞ-জ্যোতির্বিদ স্বগতোক্তি করেছিলেন-’তার পরেও কিন্তু পৃথিবী ঠিকই ঘুরছে। ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ নিয়েই গ্যালিলিওর মৃত্যু হয় ১৬৪২ সালে, নিজ গৃহে, অন্তরিন অবস্থায়। শুধু গ্যালিলিওকে অন্তরিন করে নির্যাতন তো নয়, ব্রুনোকে তো পুড়িয়েই মারলো ঈশ্বরের সুপুত্ররা। তারপরও কি সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘোরা ঠেকানো গেল?
শুধু গ্যালিলিও বা ব্রুনো নয়, ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, হাইপেশিয়া, এনাক্সোগোরাস, ফিলিগ্রাস প্যারাসেলসাস, এনাকু সিমন্ড, লুসিলিও ভানিনি, টমাস কিড, ফ্রান্সিস কেট, বার্থেীলোমিউ, লিগেট, ইবনে খালিদ, জিরহাম, আল দিমিস্কি, ওমর খৈয়াম, ইবনে সিনা, ইবনে বাজা, আল কিন্দী, আল রাজি কিংবা ইবনে রুশদসহ অনেককেই ধর্মান্ধদের হাতে নিগৃহীত এবং নির্যাতিত হয়ে নিহত হতে হয়। মুক্তমনা লেখকেরা এধরনের নিপীড়নের অনেক পরিসংখ্যান হাজির করেছেন তাদের বইপত্রে[৩৩০]।
.
বিশ্বাসের উদ্ভব
বিশ্বাসের উদ্ভব সমাজে কীভাবে হলো তা বিভিন্ন আলোচক বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করেন, করবেন, অতীতেও করেছেন। তবে আমরা-এ বইয়ের দুজন লেখক মনে করি, বিশ্বাসের পুরো ব্যাপারটিকে আসলে নৃতাত্বিক, সামাজিক এবং জৈববৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখলে বিষযের সম্পূর্ণতা আসে না। এ বইয়ে আমরা সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিশ্বাসের উদ্ভব নিয়ে আলোচনা করেছি,যা আধুনিককালে ধর্মসংক্রান্ত গবেষণার সবচাইতে অগ্রসর এবং সজীব ক্ষেত্র বলে মনে করা হয়। আমরা বইটি লিখতে গিয়ে বিশ্বাসের অবদানকে গায়ের জোরে অস্বীকার করি নি। আমরা আমাদের বইয়ে স্বীকার করেছি যে, ‘বিশ্বাস’ ব্যাপারটা মানব জাতির বেঁচে থাকার পেছনে হয়ত কোনো বাড়তি উপাদান যোগ করেছিল একটা সময়। মানুষ আদিমকাল থেকে বহু সংঘাত, মারামারি এবং রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে গিযে আজ এই পর্যায়ে এসে পোঁছেছে। একটা সময় সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করাটা ছিল মানবজাতির টিকে থাকার ক্ষেত্রে অনেক বড় নিয়ামক। যে গোত্রে বিশ্বাস ঢুকিয়ে দিতে পারা গিয়েছিল যে যোদ্ধারা সাহসের সাথে যুদ্ধ করে মারা গেলে পরলোকে গিয়ে পাবে অফুরন্ত সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, হুর পরী উদ্ভিন্নযৌবনা চিরকুমারী অপ্সরা, (আর বেঁচে থাকলে তো আছেই সাহসী যোদ্ধার বিশাল সম্মান আর পুরস্কার)–তারা হয়ত অনেক সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করেছে এবং নিজেদের এই যুদ্ধংদেহী জিন পরবর্তী প্রজন্মে বিস্তৃত করতে সহায়তা করেছে।
এই বইয়ে আমরা মানবসভ্যতাকে শিশুদের মানসজগতের সাথে তুলনা করেছি। আমরা দেখিয়েছি, শিশুদের বেঁচে থাকার প্রযোজনেই একটা সময় পর্যন্ত অভিভাবকদের সমস্ত কথা নির্দ্বিধায় মেনে চলতে হয়। শিশুরা একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত তার অভিভাবকের কথা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করে এবং পালন করে বলেই তারা বিপদ থেকে রক্ষা পায়, টিকে থাকতে পারে। কিন্তু শিশুটির অভিভাবকেরাই যথন অসংখ্য ভালো উপদেশের পাশাপাশি আবার কিছু মন্দ বা কুসংস্কারাচ্ছন্ন উপদেশও দেয়, তখন শিশুর পক্ষে সম্ভব। হয় না সেই মন্দ বিশ্বাসকে অন্য দশটা বিশ্বাস কিংবা ভালো উপদেশ থেকে আলাদা করার। সেই মন্দবিশ্বাসও বংশপরম্পরায় সে বহন করতে থাকে অবলীলায়। সব বিশ্বাস খারাপ তা আমরা বলি নি, কিন্তু আমরা বলতে চেয়েছি, অসংখ্য মন্দ বিশ্বাস হয়ত ভাইরাসের মতো একটা সময় প্রগতিকে থামাতে চায়, সভ্যতাকে ধ্বংস করে। ডাইনি পোড়ানো, সতীদাহ, বিধর্মী এবং কাফেরদের প্রতি ঘৃণা, মুরতাদদের হত্যা-এগুলোর উদাহরণ তো হাতের সামনেই আছে। এগুলো যে বিশ্বাসের প্রসারে বেড়ে ওঠা ফ্রাঙ্কেনস্টাইন ছাড়া কিছু নয়, তাতে অনেকেই একমত হবেন। কীভাবে বিশ্বাস নির্ভর ব্যবস্থা টিকে আছে, কীভাবে আমরা বিশ্বাসগুলো বংশ পরম্পরায় প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে দেই তা বুঝতে হলে সামাজিক জীববিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণাগুলোকে বুঝতে হবে। রিচার্ড ডকিন্স তার ‘সেলফিশ জিন’ বইয়ে আর সুজান ব্ল্যাকমোর তার ‘মিম মেশিন’ বইয়ে কীভাবে বিশ্বাস বংশপরম্পরায় টিকে থাকে অনেক আকর্ষণীয় উদাহরণ হাজির করেছেন। আমরাও এই বইয়ের সপ্তম এবং অষ্টম অধ্যায়ে বিশ্বাসের আধুনিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ হাজির করেছি।
মানবসভ্যতার সূচনা পর্বে ধর্ম ছিল জাদুবিদ্যা কেন্দ্রিক, অনেক নবী পয়গম্বর ছিলেন আসলে জাদুকর। বহুকাল আগে, সাভানা অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের এক গোত্রের কথা চিন্তা করা যাক। গোত্রের সব মানুষের সামনে একজন সামান, জ্বলন্ত আগুনে ছুঁড়ে দিলেন মুঠোভর্তি কালো গুড়ো। সঙ্গে সঙ্গে তীব্র বিস্ফোরণে আগুনের শিখা উপরে উঠে গেল। দর্শকদের কাছে ঘটনাটি গণ্য হলো জাদু হিসেবে। এবং এই ‘অতিপ্রাকৃত ঘটনা সবার সামনে ঘটানোর জন্য সামান নিজেকে দাবি করলেন সবার চেয়ে আলাদা। একজন, বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে। উদাহরণ হিসেবে সামনে আনা যেতে পারে সামানদের দৃষ্টান্তকে। সামান গোত্রভুক্তরা তাদের মনে থাকা অসংখ্য প্রশ্ন ও বিভিন্ন ঘটনা কে ঘটাচ্ছেন এমন প্রশ্নের উত্তর না পেযে দ্বারস্থ হতেন জাদুকর সামানদের কাছে। ইচ্ছা ছিল পেছনে থাকা একজনকে খুঁজে বের করা-যার ইশারায় ঝড় থেমে যায়, যার ইশারায় তারা খাবারের সন্ধান পায়, যার ক্রোধে মহামারীতে তাদের শত্রুপক্ষের অর্ধেকেরও বেশি লোক হুট করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সভ্যতার এই পর্যায়ে এসে আমরা দেখতে পাই, সামানরা নিজেরাও আলাদা কেউ ছিলেন না, তাদের জাদুটাও সত্যিকার অর্থে জাদু নয়, রাসায়নিক বিক্রিয়া। সামানরা নিজেদের ক্ষমতা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বানিয়ে বানিয়ে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিতেন, গোত্রের সবাই মাথা নত করে তার কথা মেনে নিতো। কখনও সূর্য, কথনও দূরে থাকা কোনো পাহাড়কে পূজা করত।
প্রথমদিকে, মানুষ ছোট ছোট গোত্রে বাস করত। তখন থেকেই সমঝোতা, ইট-মারলে পাটকেল (tit-for tat), সততা, সহমর্মিতা, বিনিময়ী পরার্থতা (Reciprocal Altruism) প্রভৃতি মূল্যবোধ প্রায় সবার মধ্যেই ছিল। গরিলা, বাদুড়, শিম্পাঞ্জি, হাতি, নেকড়ে এমনকি মৌমাছি, পিঁপড়ার মতো কিছু সামাজিক প্রাণীর মধ্যেও এই ধরনের কিছু মূল্যবোধের কম-বেশি উপস্থিতির ফলে আমরা নিশ্চিত ভাবে বুঝতে পারি, কোনো ঐশী প্রক্রিয়ায় মূল্যবোধগুলো মানবসমাজে উদ্ভূত হয় নি, বরং জৈবিক সামাজিক বিবর্তনের ফলস্বরূপ এগুলো বিবর্তনের ধারাবাহিকতাতেই উদ্ভূত হয়েছে মানুষের মধ্যে (আমরা এই বইয়ের সপ্তম অধ্যায়ে এ ব্যাপারগুলো নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি)। পরবর্তীকালে সমাজ আরও জটিল হয়েছে। সেই জটিলতা স্পর্শ করেছে নৈতিকতা আর মূল্যবোধগুলোকেও। যেমন, কৃষিকাজের ব্যাপক অগ্রগতির ফলে গোষ্ঠীভুক্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল একসময়, অপরিচিতের সাথে আদান-প্রদান, ব্যবসা বাণিজ্য শুরু হওয়ায় দেখা গেল, আগেকার সেই ছোট গোত্রের মূল্যবোধে ঠিকঠাক কাজ হচ্ছে না। এই কারণে সমাজপতি এবং নেতারা সবাইকে সংঘবদ্ধ রাখার জন্য আরও কিছু নিয়ম-কানুন সমাজে সংযুক্ত করা শুরু করলেন। তারা ভাবলেন, কেউ কিছু বললেই তো আর মানুষ শুনবে না, এই সংশযে কেউ কেউ সেই নিয়ম-কানুনগুলোকে ‘ঈশ্বর প্রদত্ত আইন’ বলে প্রচার করলেন। মধ্যপ্রাচ্যে সংঘবদ্ধ ধর্মের সূচনা তাই কোনো দুর্ঘটনা নয়, বরঞ্চ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এই অঞ্চলগুলোয় কৃষিকাজের দ্রুত উন্নতি তৈরি করেছিল যাজক শ্রেণি। সেখানকার রাজারা নিজেদের প্রকাশ করতেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে। খ্রিস্টান রাজারা চার্চের সহায়তার কারণে যেকোনো কাজ করাকে স্বর্গীয় অধিকার বলে মনে করতেন। এধরনের ঘটনা আমরা অন্য অনেক জায়গায়ই দেখি। যেমন, চীনেও একসময় রাজাকে মানবসমাজের স্বর্গীয় প্রতিনিধি হিসেবে ভাবা হতো বহুদিন।
কীভাবে নতুন ধর্ম তৈরি হয়, কীভাবে ধর্মের অনুসারী তৈরি হয়, কীভাবে মানুষ নবী রাসুলকে বিশ্বাস করতে শেখে তা একটা চমৎকার উদাহরণের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা কিন্তু দেখিয়েছেন কার্গো কাল্ট (Cargo Cult) নিয়ে গবেষণা করে[৩৩১]। ‘কার্গো কাল্ট’ হলো প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জগুলোতে বর্তমান ধর্মবিশ্বাসগুলোর একটি সম্মিলিত নাম-যারা কার্গো জাহাজগুলোকে স্বর্গীয় দূতের পাঠানো সামগ্রী মনে করত। জাহাজের ইউরোপিয়ান নাবিকেরা কীভাবে রেডিও শোনে, কেন কোনো সারাইয়ের কাজ করতে হয় না, রাতে কী করে আলো জ্বালায়-এ সবই দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীরা অদ্ভুত বিস্ময়ে দেখত। তাদের কাল্টপ্রধান জন ফ্রাম চিরতরে চলে যাওয়ার আগে সেসময় অনেকগুলো ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন দ্বিতীয়বারে জাহাজভর্তি সামগ্রী আনবে ও সাদা আমেরিকানদের চিরকালের মতো দ্বীপ থেকে বিতাড়িত করা হবে ইত্যাদি বলে। দীর্ঘ উনিশ বছর ধরে আদিবাসীরা অপেক্ষা করে আছে জন কখন আসবে তাদের মুক্তি দিতে। আপনি কি তার সাথে মিল পান বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষের মুক্তি পাওয়ার জন্য পুনরুত্থিত যিশুখ্রিস্ট কিংবা ইমাম মাহাদির জন্য অপেক্ষাকে?
.
ধর্মের কুফল
মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। মেহেদি রাঙ্গানো দাড়ির এই লোককে আমরা সবাই চিনি, বেসরকারি টিভি চ্যানেল এনটিভির অনুষ্ঠান ‘আপনার জিজ্ঞাসা’র বদৌলতো এ মানুষটি সপ্তাহান্তে আমাদের জীবনযাপনের প্রয়োজনীয় উপদেশ দেন, কীভাবে চলতে হবে তার দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তিনি কীভাবে চলেছিলেন? এখনকার মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, তখন পরিচিত ছিলেন খাড়াদ্যিার বাচ্চু নামে, তার নামে ভয়ে কাঁপতো ফরিদপুর এলাকা। ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলার যদুনন্দী ইউনিয়নের বড় বাড়দিয়া গ্রামের প্রায় শতাধিক যুবককে নিয়ে তৈরি এই মিলিটারি বাহিনী স্থানীয়দের কাছে পরিচিত ছিল, ‘থাড়দিয়ার মেলিটারি’ নামে। পাক-বাহিনীর দোসর এই বাহিনী, খাড়দিয়ার আশেপাশের প্রায় ৫০ গ্রাম জনপদে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন চালিয়েছিল তাণ্ডবলীলা। স্থানীয়দের বরাতে জানা যায়, এই বাচ্চু ও তার বাহিনী একাত্তরে নৃশংসভাবে হত্যা করে হাসামদ্যিার হরিপদ সাহা, সুরেশ পোদ্দার, মল্লিক চক্রবর্তী, সুবল ক্যাল, শরৎ সাহা, শ্রীনগরের প্রবীর সাহা, যতীন্দ্রনাথ সাহা, জিন্নাত আলী ব্যাপারী, মযেনদিয়ার শান্তিরাম বিশ্বাস, কলারনের সুধাংশু রায়, মাঝারদিয়ার মাহাদেবের মা, পুরুরার জ্ঞানেন, মাধব, কালিনগরের জীবন ডাক্তার, ফুলবাড়িয়ার চিত্তরঞ্জন দাস, ওয়াহেদ মোল্লা, দাল, মোতালেবের মা, যবদুল, বাদল নাথ, আস্তানার দরবেশসহ বিভিন্ন জনপদের প্রায় শতাধিক মানুষকে। ফতোয়া সম্পর্কিত হাইকোর্টের যুগান্তকারী রায়ের বিরুদ্ধে লিভ আবেদন কারী ও বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ বাচ্চুর বর্তমান অবস্থা দেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, নগরকান্দা উপজেলার দাদপুর ইউনিয়নের নতিবদ্যিা গ্রামের শোভা রানী বিশ্বাস। একাত্তরে তিনি এই আবুল কালাম আজাদের কাছে হয়েছিলেন ধর্ষিত। এ গ্রামেরই নগেন বিশ্বাসের স্ত্রী দেবী বিশ্বাসেরও সম্ভ্রম লুটেছিলেন বাচ্চু। নতিবদিয়ার প্রবীণ দুই মৎস্যজীবী নকুল সরদার ও রঘুনাথ দত্ত ২০০০ সালে প্রকাশিত জনকণ্ঠের ‘তুই রাজাকার’ শীর্ষক ধারাবাহিক রিপোর্টের রিপোর্টার প্রবীর সিকদারকে জানান লুটপাট-হামলা না করার শর্তে আমরা চাঁদা তুলে বাচ্চুকে দু’হাজার চার শ’ টাকা দিয়েছিলাম। তারপরও সে লুটপাট করেছে, গ্রামের দুই নববধূকে ইজ্জত হরণ করেছে। পুরুরা গ্রামের জ্ঞানেন জীবন বাঁচাতে পুকুরে ঝাঁপ দিয়ে কচুরিপানার নিচে আশ্রয় নিয়েছিল। বাচ্চু সেখানেই তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। বাচ্চুর রাইফেলের গুলিতে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারান ফরিদপুরের ফুলবাডিয়ার চিত্তরঞ্জন দাস। সেদিন তার অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী জ্যোৎস্না পালিয়ে রক্ষা পেলেও একাত্তরে বিনা চিকিৎসায় মারা যায় তার তিন শিশু সন্তান। স্বাধীনতা পরবর্তী দীর্ঘদিন জ্যোৎস্না শুধু তার স্বামী হন্তারকের বিচার চেয়েছিলেন মনে মনে। উল্লেখ্য, ২০০০ সালে সাংবাদিক প্রবীর সিকদার দৈনিক জনকণ্ঠে বাচ্চুসহ ফরিদপুর অঞ্চলের রাজাকারদের নিয়ে ‘তুই রাজাকার’ শীর্ষক প্রামাণ্য সিরিজ প্রতিবেদন করায় তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে অস্ত্র, গুলি ও বোমা হামলা চালানো হয়। এ হামলার পেছনে তখন কুখ্যাত রাজাকার নুলা মুসা ও বাঙুর ইন্ধনের অভিযোগ ওঠে[৩৩২]।
ধর্ম না থাকলেও হয়ত, মুক্তিযুদ্ধে আবুল কালামের মতো লোকেরা নিরাপরাধী লোকদের ধরে ধরে হত্যা করত। কিন্তু ধর্ম থাকাতে একাত্তরে অসংখ্য বিধর্মীদের প্রাণ দিতে হয়েছে মাওলানা আজাদের পুণ্য কাজের খেসারত স্বরূপ আজাদরা মনে মনে শান্তি পেয়েছেন। পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তানকে ভাঙ্গনের হাত থেকে রক্ষার জন্য তারা আল্লাহর হয়ে কাজ করছেন ভেবে। সেটাও হলো, কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপারটা আসে আরও পরে। হুমায়ুন আজাদ বলেছিলেন, এদেশের মুসলমান একসময় ছিলেন মুসলমান বাঙালি, তারপর বাঙালি মুসলমান, তারপর বাঙালি হয়েছিল; এখন আবার তারা বাঙালি থেকে বাঙালি মুসলমান, বাঙালি মুসলমান থেকে মুসলমান বাঙালি, এবং মুসলমান বাঙালি থেকে মুসলমান হচ্ছেন। পৌত্রের ঔরসে জন্ম নিচ্ছে পিতামহ। হুমায়ুন আজাদ সত্যিই বলেছিলেন, তা না হলে আবুল কালাম আজাদদের হাত থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষা করে আমরা নৈতিকতার সন্ধানের জন্য তাদের কাছেই ফিরে যাচ্ছি কেন? ধর্ম যতই নৈতিকতাকে ভাই বা অবিচ্ছেদ্য কেউ বলুক না কেন, নৈতিকতার চরম স্থলনে সর্বদাই সচেষ্ট ভূমিকা পালন করেছে ধর্ম। পার্থক্য এই যে চরম স্থলনকেও ধার্মিকরা ভেবেছেন চরম ভালো কোনো কাজ হিসেবে আমরা পুরো ব্যাপারটিকে ব্যাখ্যা করেছি বইয়ের সপ্তম অধ্যায়ে বিজ্ঞানী স্টিফেন ভাইনবার্গের একটি চমৎকার উদ্ধৃতি দিয়ে–
ধর্ম মানবতার জন্য এক নির্মম পরিহাস। ধর্ম মানুক বা নাই মানুক, সবসময়ই এমন অবস্থা থাকবে যে ভালো মানুষেরা ভালো কাজ করছে, আর খারাপ মানুষেরা খারাপ কাজ করছে। কিন্তু ভালো মানুষকে দিয়ে খারাপ কাজ করানোর ক্ষেত্রে ধর্মের জুড়ি নেই।
ব্লগে লেখালেখি করতে গিয়ে ধর্মের কুফল নিয়ে আলোচনা শুরু করে অনেক ধার্মিকই নাস্তিকদের উদাহরণ হিসেবে হিটলার স্ট্যালিন, মাও কিংবা পল পটের মতো দাম্ভিক ডিক্টেটরের কথা নিয়ে এসে প্রসঙ্গ অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিতে সচেষ্ট হন। তারা হিটলার, স্ট্যালিন প্রমুখের উদাহরণ টেনে বুঝিয়ে দিতে চান যে, ধর্মের মতো নাস্তিকতার কুফলও কম নয়।
হিটলার এবং স্ট্যালিনের প্রসঙ্গে আসা যাক। হিটলার কখনোই নাস্তিক ছিলেন না। হিটলার নিজেই তার বই ‘Mein Kampf’-এ বলেছেন তার ইহুদি নিধনের কিংবা এধরনের যাবতীয় কাজকর্মের পেছনে অনুপ্রেরণা ছিল স্বয়ং ঈশ্বর[৩৩৩]–
Hence today I believe that I am acting in accordance with the will of the Almighty Creator : by defending myself against the Jew, I am fighting for the work of the Lord.
নিজেকে ভালো খ্রিস্টান হিসেবে পরিচিত করে হিটলার তার বিভিন্ন বক্তৃতা দিয়েছেন। হিটলারের একটি বক্তৃতা থেকে উদ্ধৃত করা যাক প্রাসঙ্গিক কিছু[৩৩৪]–
My feelings as a Christian point me to my Lord and Savior as a fighter. It points me to the man who once in loneliness, surrounded by a few followers, recognized these Jews for what they were and summoned men to fight against them and who, God’s truth! was greatest not as a sufferer but as a fighter. In boundless love as a Christian and as a man I read through the passage which tells us how the Lord at last rose in His might and seized the scourge to drive out of the Temple the brood of vipers and adders. How terrific was His fight for the world against the Jewish poison. To-day, after two thousand years, with deepest emotion I recognize more profoundly than ever before the fact that it was for this that He had to shed His blood upon the Cross. As a Christian I have no duty to allow myself to be cheated, but I have the duty to be a fighter for truth and justice… And if there is anything which could demonstrate that we are acting rightly it is the distress that daily grows. For as a Christian I have also a duty to my own people.
প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রিস্টান নেতা মার্টিন লুথারের ইহুদিদের প্রতি বিদ্বেষমূলক গ্রন্থ ‘On the Jews and their Lies যে হিটলারকে দারুণভাবে উদ্দীপ্ত করেছিল, তাও ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত[৩৩৫]।
আর স্ট্যালিন নাস্তিকতা প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের বিরোধী লোকজনের ওপর খুন, জখম, জেল-জুলুম করেন নি, সেগুলো করেছিলেন কমিউনিস্ট মতাদর্শ প্রতিষ্ঠার নামে[৩৩৬]। আর তারচেযেও মজার ব্যাপার হলো, কমিউনিস্ট রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নে দাপ্তরিকভাবে ধর্মকে অস্বীকার করা হলেও, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্ট্যালিন রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্চের সাথে সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন। ইতিহাসবিদ এডভার্ড রেন্সিকি ( Edvard Radzinsky) তার গবেষণায় দেখিয়েছেন, স্ট্যালিনের সরকারের সাথে চার্চের সবসময়ই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল[৩৩৭]। এই সম্পর্ক এমনি এমনি তৈরি করা হয় নি, হয়েছিল এক শ্রেণির মানুষকে চার্চের সহায়তায় দমিয়ে রাখার জন্য, যারা রাষ্ট্রীয় চিন্তাভাবনার প্রতি চরম আনুগত্য প্রকাশ করে নি। শতবছর ধরে রাশিয়ান অর্থোডক্স চার্টের সাথে জারিষ্ট সিক্রেট পুলিশের গোপন সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, সুতরাং এটা অবাক হওয়ার মতো কোনো ব্যাপার না যে, স্ট্যালিন এবং বর্তমান রাশিয়ার প্রধান সাবেক কেজিবি কর্মকর্তা ম্লাদিমির পুতিন অর্থোডক্স চার্চকে হাতে রেখেছেন। এদের কাজের জন্য নাস্তিকতাকে দায়ী করা সমীচীন নয়। বার্ট্রান্ড রাসেল, রিচার্ড ডকিন্স কিংবা স্টিফেন ওয়াইনবার্গ-এদের মতো ব্যক্তিত্বরাও নিজেদের নাস্তিক হিসেবে পরিচিত করেন এবং নাস্তিকতা প্রচার করেন কোনো রকম রাখঢাক না রেখেই-কিন্তু কই তারা তো খুন রাহাজানি বা গণহত্যা করেন নি কিংবা করছেন না। নাস্তিকতা কোনো বিশ্বাসের ব্যাপার নয়[৩৩৮]। নাস্তিকদের কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই, যেটা তারা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন, তাই ধর্মগ্রন্থের প্রেরণায় লাদেন, স্ট্যালিন, হিটলার, আল কায়দা কিংবা বজরংদলদের মতো নাস্তিকেরাও মানুষ হত্যায় উজ্জীবিত হয়ে উঠবেন তা মনে করা ভুল। নাস্তিকদের ম্যানুয়ালে লেখা নাই যেখানেই পাও ইহুদি নাসারাদের হত্যা কর’, কিন্তু বহু ধর্মের ম্যানুয়ালেই আছে। নাস্তিকেরা যে অপরাধ করেন না তা নয়, কিন্তু সেগুলো নাস্তিকতার কারণে করেন না, হয়ত করেন কোনো ব্যক্তিগত কারণে কিংবা কোনো রাজনৈতিক কারণে, নাস্তিকতার জন্য নয়।
হিটলার-স্ট্যালিনের ব্যাপারটা আরও সরলভাবে বোঝানো যায়। স্ট্যালিন এবং হিটলার দুজনেরই গোঁফ ছিল। এখন কেউ যদি যুক্তি দেন গোঁফ থাকার জন্যই তারা গণহত্যা করেছেন, কিংবা গোঁফওয়ালা ব্যক্তিরাই গণহত্যা করে-এটা শুনতে যেমন বেখাপ্পা এবং হাস্যকর শোনাবে, ঠিক তেমনই হাস্যকর শোনায় কেউ যখন বলেন, নাস্তিকতার জন্যই কেউ স্ট্যালিন বা হিটলারের মতো গণহত্যা করেছেন।
.
সেকুলারিজম মানে কি সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা?
এই গ্রন্থের দুই লেখককেই মুক্তমনাসহ অন্যান্য ব্লগে বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে লিখতে, আলোচনা করতে এবং বিতর্কে অংশ নিতে হয়। ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়টিও মাঝে মধ্যে চলে আসে। বিতর্ক করতে গিয়ে অনেকের কাছ থেকেই যা শোনা যায় তা হলো, সেকুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দের মানে হচ্ছে সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা। এমনকি যারা ধর্ম মানেন না, এবং উদারপন্থী বলে কথিত তাদের অনেকেই ধর্মনিরপেক্ষতাকে এভাবে দেখেন।
বিষয়টি আলোচনার দাবি রাখে। সেকুলার শব্দের মানে কি সত্যিই সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা? অন্তত রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলাদেশ কিংবা ভারতের মতো দেশগুলোতে এখন তা-ই প্রচার করা হয়। বিভ্রান্তি সে কারণেই। আসলে কিন্তু ‘সেক্যলারিজম’ শব্দটির অর্থ ‘সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা নয়, বরং এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে একটি মতবাদ, যা মনে করে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি থেকে ধর্মকে পৃথক রাখা উচিত। আমেরিকান হেরিটেজ ডিকশনারিতে secularism শব্দটির সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে এভাবে–
The view that religious considerations should be excluded from civil affairs or public education
এ সংজ্ঞা থেকে বোঝা যাচ্ছে, ধর্মকে রাষ্ট্রের কাজের সাথে জড়ানো যাবে না এটাই সেকুলারিজমের মোদ্দা কথা। ধর্ম অবশ্যই থাকতে পারে, তবে তা থাকবে জনগণের ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলে প্রাইভেট ব্যাপার হিসেবে; ‘পাবলিক’ ব্যাপার স্যাপারে তাকে জড়ানো যাবে না।
ভারত তার জন্মলগ্ন থেকেই ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’কে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করে এসেছে (যদিও ভারতের সংবিধানে ‘অফিশিয়ালি’ ধর্মনিরপেক্ষতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অনেক পরে)। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু সেকুলারিজমের প্রকৃত সংজ্ঞা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন অনেক ভালোভাবে। তিনি রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী থেকে ধর্মকে পৃথক রাখাই সংগত মনে করতেন, জাতীয় জীবনে সব ধর্মের প্রতি উদাসীন থাকাটাই তার কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হতো। তিনি বলতেন–
ধর্ম বলতে যে ব্যাপারগুলোকে ভারতে কিংবা অন্যত্র বোঝানো হয়, তার ভয়াবহতা দেখে আমি শক্ষিত এবং আমি সবসময়ই তা সোচ্চারে ঘোষণা করেছি। শুধু তাই নয়, আমার সবসময়ই মনে হয়েছে এ জঞ্জাল সাফ করে ফেলাই ভালো। প্রায় সব ক্ষেত্রেই ধর্ম দাঁড়ায় ধর্মান্ধতা, প্রতিক্র্যিাশিলতা, মূঢ়তা, কুসংস্কার আর বিশেষ মহলের ইচ্ছার প্রতিভূ হিসেবে।
আমেরিকার ‘ফাউন্ডিং ফাদার’দের মাঝে নেহেরুর অনুপ্রেরণা ছিল কিনা জানি না, তবে তারা আমেরিকার সংবিধান তৈরির সময় ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা রেখেছিলেন, খুব বলিষ্ঠ ভাবে[৩৩৯]–
As the Government of the United States of America is not, in any sense, founded on the Christian religion; as it has in itself no character of enmity against the laws, religion, or tranquility, of Musselmen; and as the said States never have entered into any war or act of hostility against any Mehomitan nation, it is declared by the parties that no pretext arising from religious opinions shall ever produce an interruption of the harmony existing between the two countries. (ref. The Treaty of Tripoli, drafted in 1796 under George Washington, and signed by John Adams in 1797)
আসলে অভিধানে secular শব্দটির অর্থও করা হয়েছে 2015 ‘Worldly rather than spiritual’ সেকুলারিজমের অন্যান্য প্রতিশব্দগুলো হলো worldly, temporal কিংবা profanel শব্দার্থগুলো খুব ভালোভাবে খেয়াল করলে বোঝা যাবে, এর অবস্থান ধর্ম কিংবা আধ্যাত্মিকতার দিকে নয়, বরং এর একশ আশি ডিগ্রি বিপরীতে। সেজন্য, সেকুলারিজমের বাংলা প্রতিশব্দ অনেকে খুব সঠিকভাবেই করেন ‘ইহজাগতিকতা।
অথচ সেই ‘ইহজাগতিক’ ভারতেই রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণণ পঞ্চাশের দশকে ঘোষণা করলেন, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয় বরং সর্ব ধর্মের সহাবস্থান, এবং Hindu view of life-এর কল্পিত ভাববাদী পূর্ণতায় তিনি আস্থাবান। ‘ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়’-এই শ্লোগানটি বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারী দল আওয়ামী লীগও খুব জোরেশোরে বলার চেষ্টা করে। তবে এ শ্লোগানটির মধ্যেই রয়েছে এক ধরনের ‘শুভঙ্করের ফাঁকি’। এ ফাঁকিটি চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তার ‘ইহজাগতিকতার প্রশ্ন’ প্রবন্ধে। এ প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছে অভিজিৎ রায় আর সাদ কামালীর যৌথ সম্পাদনায় প্রকাশিত ‘স্বতন্ত্র ভাবনা’ (চারদিক, ২০০৮) বইয়ে–
ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়, এই কথাটা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর পরই খুব জোরেশোরে বলা হচ্ছে। কথাটা সত্য বটে আবার মিথ্যাও বটে। সত্য এ দিক থেকে যে, রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা নাগরিকদের এ পরামর্শ দেয় না যে, তোমাদের ধর্মহীন হতে হবে; কিন্তু তা বলে এমন কথাও বলে না যে, রাষ্ট্র নিজেই সকল ধর্মের চর্চা করবে, কিংবা নাগরিকদের নিজ নিজ ধর্ম চর্চায় উৎসাহিত করবে। রাষ্ট্র বরঞ্চ বলবে ধর্মচর্চার ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিজের কোনো আগ্রহ নেই, রাষ্ট্র নিজে একটি ধর্মহীন প্রতিষ্ঠান। ধর্ম বিশ্বাস নাগরিকদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। রাষ্ট্রের ওই ধর্মহীনতাকেই কিছুটা নম্রভাবে বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষতা।
আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের প্রধানতম রাজনৈতিক দল, যারা নীতিগতভাবে এদেশে ধর্মনিরেপক্ষতা প্রতিষ্ঠা করতে সোচ্চার, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, তারাও ধর্মনিরপেক্ষতার মূল সুরটি কখনোই অনুধাবন করতে পারে নি। তার প্রমাণ পাওয়া যায় আওয়ামী লীগের ওয়েবসাইট (http://www.albd.org/) দেখলেই। আওয়ামী লীগের ওয়েবসাইটে মাথার উপরে আল্লাহ সর্বশক্তিমান’ লেখাটি ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতারই পরিচয় বহন করে। অথচ এক সময় আওয়ামী লীগই ‘আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি উঠিয়ে দেওয়ার সাহস দেখাতে পেরেছিল কিংবা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার অব্যবহিত পরে ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। সেসময় রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলো ছিল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। মুক্তিযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে খুব স্বাভাবিক ছিল সে অঙ্গীকার। কিন্তু এর জন্য যে বিশাল সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা প্রয়োজন তা সে সময়কার নেতাদের যথেষ্ট পরিমাণে ছিল কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।
ধর্মনিরপেক্ষতাকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করলেও এর মূল ভাবটি তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে স্পষ্ট ছিল- এমন কোনো নজির পাওয়া যায় নি। পাকিস্তানি কারাগার থেকে ঢাকায় ফিরে এসে রেসকোর্স ময়দানে বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যে বক্তৃতা দেন তাতে তিনি বাংলাদেশকে ‘দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন তা কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। ওই বছরেরই সাতই জুন তারিখের বক্তৃতায় শেখ মুজিবুর রহমান ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে যা বলেছেন তা হলো–
বাংলাদেশ হবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। মুসলমান মুসলমানের ধর্ম পালন করবে, হিন্দু হিন্দুর ধর্ম পালন করবে। খ্রিস্টান তার ধর্ম পালন করবে। বৌদ্ধও তার নিজের ধর্ম পালন করবে। এ মাটিতে ধর্মহীনতা নেই, ধর্মনিরপেক্ষতা আছে।
এ বক্তৃতা থেকে শেখ মুজিবের ‘সর্বধর্মের প্রতি সদ্ভাবের সুর ধ্বনিত হলেও সেকুলারিজমের মূল সুরটি অনুধাবিত হয় নি। আর হয় নি বলেই, সেসময়কার সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদে ‘ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করার সুযোগ লোপ করা হলেও, প্রবণতা দেখা দিল রাষ্ট্রকর্তৃক সকল ধর্মকে সমান মর্যাদাদানে। তাই বেতারে, টেলিভিশনে, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে সর্বত্র কোরআন শরীফ, গীতা, বাইবেল আর ত্রিপিটক পাঠ করা হতে লাগলো এক সঙ্গে। এ আসলে প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা নয়, বরং ধর্ম আর শ্রদ্ধার মিশেল দেওয়া এক ধরনের জগাখিচুড়ি। সহজ ভাষায় বলা যেতে পারে ‘চম-ধর্মনিরপেক্ষতা’। যত দিন গেছে, ততই শেখ মুজিব এমনকি এই ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতা থেকেও দূরে সরে গেছেন। তার শাসনামলের প্রান্তে প্রতিটি ভাষণেই মুজিব ‘আল্লাহ’, ‘বিসমিল্লাহ’, ‘ইনশাল্লাহ’, ‘তওবা” প্রভৃতি শব্দ উচ্চারণ করতেন। এমনকি শেষদিকে মুক্তিযুদ্ধের স্মারক প্রতীক ‘জয় বাংলা’ও বাদ দিয়ে ‘খোদা হাফেজ’ প্রবর্তন করেন। শুধু তাই নয়, যে। ‘ইসলামিক অ্যাকাডেমি’ মুক্তিযুদ্ধের সময় রাজাকার আলবদরদের সাথে ঘনিষ্ঠতার কারণে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল, তারও পুনরুত্থান ঘটান শেখ মুজিব এবং প্রতিষ্ঠানটিকে ‘ফাউন্ডেশন’-এ উন্নীত করেন।
তাও কাগজে কলমে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা সংবিধানে যাওবা চালু ছিল মুজিবের সময়, জিয়াউর রহমান এসে তা মূল সুদ্ধ উপড়ে ফেললেন। ধর্মনিরপেক্ষতার উপরে কাঁচি চালিয়ে অন্তর্ভুক্ত করা হলো ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ আর সমান বেগে মূলনীতি হিসেবে স্থাপিত হলো ‘সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর আস্থা আর বিশ্বাস’কে। সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদ-এর উচ্ছেদ হয়ে গেল। ১২ নং অনুচ্ছেদের উচ্ছেদের ফলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করার সুযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো। এরশাদ সাহেব এসে তো ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্মই বানিয়ে দিলেন। এরপর থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা তো অচ্ছুৎ হয়েছেই, বরং পাল্লা দিয়ে শুরু হয়েছে ধর্মকে তোষণ করে চলার নীতি। বিগত জোট সরকারের আমলে ধর্মকে আর মৌলবাদকে তোষণ করার ফলস্বরূপ কীভাবে বাংলা ভাইযের উত্থান হয়েছিল, কীভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর পরিকল্পিতভাবে নির্যাতন চালানো হয়েছিল, কীভাবে প্রতিটি জেলায়, সিনেমা হলে, মাজারে, উদীচীর অনুষ্ঠানে বোমাবাজির মহড়া চালানো হয়েছিল তা আমরা সবাই দেখেছি।
জনগণকে ইহজাগতিকতায় উদ্বুদ্ধ করার কাজ অতীতের শাসকেরা করে নি, এখনকার শাসকেরাও করছেন না। মোহাম্মদ বিড়াল’ নিয়ে আলপিন নাটক আর তার পরিসমাপ্তি বায়তুল মোকারমের খতিবের কাছে গিযে ক্ষমা প্রার্থনার মহড়া আমরা দেখেছি কিছুদিন আগে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে। এতদিন রাষ্ট্রীয় বিবাদ-বিপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সংসদভবন, বঙ্গভবন এগুলো ছিল উপযুক্ত এবং নির্বাচিত স্থান। আমাদের অতি বুদ্ধিমান রাষ্ট্রের কর্ণধাররা সেটিকে সংসদ ভবনের বদলে বায়তুল মোকারমের বৈঠকখানায় নিয়ে উঠালেন। পরে দেখলাম, ‘জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের পরিবর্তে অর্ধশিক্ষিত, শিক্ষিত মোল্লাগোষ্ঠীকে তোষণ করে চললেন সেসময়কার শাসকেরা। দেখেছি ‘ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগার অজুহাতে ফেসবুক বন্ধের নাটক এবং তারপর আবার জনদাবির মুখে খুলে দেওয়ার নির্লজ্জ তামাসা।
ভারতের অবস্থাও যে খুব ভালো তা বলা যাবে না। সেখানেও সেকুলারিজমের মূল সুরটি আত্মস্থ করার পরিবর্তে চলছে ছদ্ম-ধর্মনিরপেক্ষতা জাহির করার মহড়া। এ প্রসঙ্গে প্রবীর ঘোষ তার সংস্কৃতি, সংঘর্ষ ও নির্মাণ’ বইয়ে লিখেছেন–
বিপুল প্রচারে সাধারণ মানুষ পরিচিত হয়েছে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শব্দের সাথে। জেনেছে, ধর্মনিরপেক্ষতা কথার অর্থ হলো ‘সব ধর্মের সমান অধিকার। বিপুল সরকারি অর্থব্যযে ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দের এই যে ব্যাখ্যা হাজির করা হচ্ছে এবং এরই সাথে সম্পর্কিতভাবে আমাদের দেশের মন্ত্রী, আমলা ও রাজনীতিকরা মন্দিরে মন্দিরে পুজো দিয়ে বেড়াচ্ছেন, গুরুদোয়ারায় নতজানু হচ্ছেন, মসজিদে গির্জায় শ্রদ্ধা জানিয়ে আসছেন। দেওয়ালী, ঈদ, বড়দিন ইত্যাদিতে রাষ্ট্রনায়কেরা বেতার, দূরদর্শন মারফৎ শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য দিলে আয়কর থেকে রেহাইযের ব্যবস্থা করে দিচ্ছেন।
সাধারণের ভালো লাগছে ‘সব ধর্মের সমান অধিকার মেনে নিয়ে মন্ত্রী, আমলা, রাজনীতিকদের সমস্ত ধর্মের কাছে নতজানু হতে দেখে। উদার হৃদয়ের মানুষ হিসেবে নিজেদের ভাবতে ভালো লাগছে জনগণের হুঁ হুঁ বাবা, আমাদের দেশ ধর্মনিরপেক্ষ। এখানে সব ধর্মই সমান। অধিকার ও শ্রদ্ধা পায় মন্ত্রী আমলাদের। মন্ত্রীরা এরই মাঝে জানিয়ে দেন সমস্ত ধর্মের সমান অধিকার বজায় রাখতে, দেশের ‘ধর্মনিরপেক্ষতার মশাল জ্বালিয়ে রাখতে হবে।
‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ শব্দটিকে নিয়ে কী নিদারুণভাবে অপব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষের মগজ ধোলাই করা হচ্ছে ভাবা যায় না। ‘নিরপেক্ষ’ শব্দের অর্থ কোনো পক্ষে নয়। ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ শব্দের অর্থ তাই কোনো ধর্মের পক্ষে নয়’-অর্থাৎ, সমস্ত ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জিত। Secularism শব্দের আভিধানিক অর্থ একটি মতবাদ যা মনে করে রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষানীতি প্রভৃতি ধর্মীয় শাসন থেকে মুক্ত থাকা উচিত।
কিন্তু এ কী! এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে আমরা কী দেখাচ্ছি? সেকুলার রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানেও এদেশে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। কোনো প্রকল্পের উদ্বোধন বা শিলান্যাস করা হয় মন্ত্রোচ্চারণের প্রদীপ জ্বালিযে, পুস্পার্ঘ্য নিবেদন করা হয় নারকোল ফাটিযে। রাজনীতির ব্যবসায়ীরা ‘সেকুলারিজম’-এর নামে নানা ধর্মকে তোল্লাই দিয়ে সর্বধর্মের সমন্বয় ও সংহতির বাঁধা গৎই এতদিন বাজিয়ে এসেছেন।
কিন্তু এই ছদ্ম-নিরপেক্ষতা যে ভারতের কোনো উপকারে আসে নি ইতিহাস তার প্রমাণ। জাতিভেদ প্রথা, ধর্মীয় সংঘাত আর দাঙ্গা সে স্বরূপটিই আমাদের সামনে তুলে ধরে। শাহবানু মামলায় আমরা দেখেছিলাম কিভাবে ১৯৮৬ সালে রাজীব গান্ধী সরকারের তথাকথিত ভারতীয় ‘ধর্মনিরপেক্ষতা’ নতজানু হয়েছিলো ইসলামিক শরিয়ার কাছে। গুটিকয় মুসলিম মৌলবাদীদের আন্দোলনের চাপে তাদের ভোট ব্যাংককে অক্ষত রাখতে অসহায় শাহবানুর মানবাধিকার লঙ্ঘন করতে কার্পণ্য করেনি সেসময়কার কংগ্রেস পার্টি। কিছুদিন আগে ‘রাম জন্মভূমি’কে পুঁজি করে বাবরি মসজিদ ধ্বংস, অযোধ্যায় নির্বিচারে মুসলিমদের হত্যা, গুজরাটে দাঙ্গা আর তার ফলে ধর্মান্ধ বিজেপির উত্থান আমাদের কাছে ঐ ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতার স্বরূপ উৎকটভাবে প্রকাশ করে দিয়েছে। গুজরাট দাঙ্গার পর অধ্যাপক জয়ন্তী প্যাটেল তার ‘India : Gujarat riots-communalization of state and civic society প্রবন্ধে যে মন্তব্য করেছেন, তা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ–
Our interpretation of secular as SARVADHARMA SAMABHAV, protecting every religion and their diverse mode of belief structure, their separate social and civil code, varied customs, mores and faiths, and even education system is not conducive in building an integrated national society or human identity. Our identity is basically communal and has proved to be an obstruction in building a nation-state. It is clear that in interpreting the meaning of the word secular we have disregarded the spirit of the enlightenment and renaissance which was instrumental in building a modern state and the civic society in the west. It seems that we have to interpret the correct meaning of the word secular in our law enforcement. The connotation of the word secular should mean negation of all religions (SARVADHARMA-ABHAV).
রেনেসাঁর মানব মুক্তি প্রয়াস কিন্তু তখনকার সময়ের গির্জাকেন্দ্রিক ধর্মের গোঁড়ামিকে উপেক্ষা করেই পরিচালিত হয়েছিল। সেকুলারিজম বলতে সেখানে সব ধর্মের সহাবস্থান বোঝানো হয় নি। ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ ফ্রান্সকে ধর্মনিরপেক্ষ থাকার প্রেরণা জুগিয়েছে। আদি বসতি স্থাপনকারীদের ধর্মীয়ভাবে নিপীড়িত হওয়ার অভিজ্ঞতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে কোনো বিশেষ ধর্মের পক্ষ নিতে দেয় নি। আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের জীবনে মুক্তিযুদ্ধের মতো এত বড় ধরনের ঘটনা ঘটলেও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত তাৎপর্য আমরা পঁয়ত্রিশ বছরেও অনুধাবন করতে পারলাম না। সনৎ কুমার সাহার একটি উদ্ধৃতি এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য–
সেকুলারিজম বহু শতাব্দী ধরে (আমাদের উপমহাদেশে) যেভাবে আচরিত এবং রূপান্তরিত হয়ে আসছে, ‘ধর্মনিরপেক্ষতাকেই যদি তার ঠিক বঙ্গানুবাদ বলে ধরে নেই, তবে শুধু সব ধর্মের সহাবস্থানেই তার অর্থ পুরোপুরি ধরা পড়ে না। এ কথা সত্য যে, ধর্মনিরপেক্ষতায় তার প্রয়োজন আছে, কিন্তু তা যথেষ্ট নয়; ধর্ম থেকে চিন্তার মুক্তিতেই ধর্মনিরপেক্ষতা পূর্ণতা পায়।
ধর্ম থেকে চিন্তার মুক্তি ব্যক্তিগত পর্যায়ে না হলেও, রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে অন্তত জরুরি। ব্যাপারটি রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা যত তাড়াতাড়ি উপলব্ধি করবেন, ততই মঙ্গল।
.
ধর্মহীন সমাজ
চরমপন্থি ধার্মিকরা প্রায় বলে বেড়ান নাস্তিকতা এবং ধর্মনিরপেক্ষতা সমাজের ভিত্তিকে ধ্বংস করে দিবে। বাংলাদেশের মোল্লারা ওয়াজ মাহফিলে জ্বালাময়ী কণ্ঠে ব্যাখ্যা করেন, ধর্মনিরপেক্ষতা কীভাবে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশকে। মার্কিন টেলিভাজেলিস্ট প্যাট রবার্টসন ধর্মহীন সমাজ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, ‘ফলাফল হবে স্বেচ্ছাচারতন্ত্র কাযেম। আমরা বইয়ের সপ্তম অধ্যায়ে ধর্মহীন সমাজ নিয়ে আমেরিকার এরকম কট্টরপন্থী লেখক লেখিকাঁদের মনোভাবের উল্লেখ করেছি। যেমন-এন কোলটার তার বই ‘গডলেস’-এ বলেন, যে সমাজ ঈশ্বরের মর্যাদা বুঝতে অপারগ সেই সমাজের গন্তব্য দাসত্ব, গণহত্যা, বর্বরতা, নিষ্ঠুরতার দিকে। তিনি আরও বলেন, যে সমাজে বিবর্তন সাধারণের কাছে সত্য বলে গণ্য সেই সমাজে নৈতিকতার স্থান কবরে। ফক্স নিউজের জনপ্রিয় উপস্থাপক বিল ও’রেইলির উদ্ধৃতিও আমরা দিয়েছি যেখানে তিনি বলেন, যে সমাজ ঈশ্বরের ছায়াতলে থাকতে ব্যর্থ সেই সমাজে আছে শুধু ‘নৈরাজ্য আর দুর্নীতি’, যেখানে ‘আইন অমান্যকারীরা ঘুরে বেড়ায় বহাল তবিয়তে[৩৪০]।
ব্রিটিশ ধর্মবেত্তা কেইথ ওয়ার্ড বলেন, যে সমাজ প্রবল ধর্মীয় রীতিনীতি মেনে সে সমাজ অনৈতিক, পরাধীন এবং অস্থিতিশীল[৩৪১]। দার্শনিক জন ডি. কাপুটো ঘোষণা করেন, ধর্মহীন মানুষ এবং ঈশ্বরকে ভালো না বাসা মানুষরা স্বার্থপর এবং অভদ্র, সুতরাং তাদের দিয়ে গড়া সমাজ ভালোবাসাহীন জঘন্য স্থান[৩৪২]
প্রত্যেকবারের মতো আবারও আমরা দেখতে পাই, ধার্মিকরা কেমন করে প্রমাণ অগ্রাহ্য করে, বাস্তবতাকে পাশ কাটিয়ে নিজেদের বিশ্বাসের পক্ষে থাকেন। অন্ধবিশ্বাস আসলে এভাবেই কাজ করে। কোনো প্রমাণ গ্রাহ্য করে না, গ্রাহ্য করে না বাস্তবতা। আমরা সপ্তম অধ্যায়ে বহু জরিপ এবং পরিসংখ্যান হাজির করে দেখিয়েছি যে, এমন কোনো বৈজ্ঞানিক উপাত্ত বা ডেটা পাওয়া যায় নি যা থেকে প্রমাণিত হয় যে, অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের চাইতে বেশি অপরাধপ্রবণ; বরং কিছু পরিসংখ্যান একেবারেই উল্টো সিদ্ধান্ত হাজির করেছে। বেশকিছু দেশে চালানো বহু জরিপেই পাওয়া গেছে যে, সেখানকার জনসাধারণের মধ্যে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ ধর্মহীন হওয়া সত্বেও তাদের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা কম, বিশ্বাসীদের মধ্যেই বরং অপরাধপ্রবণতা বেশি, হত্যা, খুন রাহাজানি এমনকি বিবাহবিচ্ছেদ থেকে শুরু করে শিশুনির্যাতনও। আজকে যেসব সমাজের অধিকাংশ ধর্ম থেকে মুক্ত, মুক্ত ঈশ্বর থেকে সেসব সমাজ ঘৃণ্য, জঘন্য, হানাহানিতে পরিপূর্ণ তো দূরের কথা এগুলো পৃথিবীর অন্যতম সুখী, নিরাপদ, সফল সমাজ।
আমরা বইয়ের সপ্তম অধ্যায়ে সমাজবিজ্ঞানী ফিল জুকারম্যানের অভিজ্ঞতাও বর্ণনা করেছি। তিনি ২০০৫ ০৬ সালে চোদ্দ মাস ধরে ডেনমার্ক ও সুইডেনে অবস্থান করে ধর্ম ও ঈশ্বর-সংক্রান্ত বিষয়ে অসংখ্য মানুষ। সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন। তার ২০০৮-এর বই ‘Society without God’-এ[৩৪৩] এই সাক্ষাৎকারের ফল তিনি প্রকাশ করেন।
বেশিরভাগ ড্যানিশ এবং সুইডিশ ধর্ম দ্বারা সংজ্ঞায়িত ‘সিন’ বা পাপ নামক কোনো ব্যাপারে বিশ্বাসী নন অথচ দেশ দুটিতে অপরাধ প্রবণতার হার পৃথিবীর সকল দেশের তুলনায় সর্বনিম্ন। এই দুই দেশের প্রায় কেউই চার্চে যায় না, পড়ে না বাইবেল। তারা কি অসুখী? ৯১টি দেশের মধ্যে করা এক জরিপ অনুযায়ী, সুখী দেশের তালিকায় ডেনমার্কের অবস্থান প্রথম, যে ডেনমার্কে নাস্তিকতার হার মোট জনসংখ্যার প্রায় শতকরা আশি ভাগ। স্ক্যান্ডিনেভিযায় মাত্র ২০ শতাংশের মতো মানুষ ঈশ্বরের বিশ্বাস করেন, তারা মনে করেন ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশ্বাস করেন, মৃত্যুর পরের জগতে। আর বাকিরা স্রেফ কুসংস্কার বলে ছুঁড়ে ফেলেছেন এ চিন্তা।
ঈশ্বরহীন এইসব সমাজের অবস্থা তবে কেমন? সমাজের অবস্থা মাপার সকল পরিমাপ-গড় আয়ু, শিক্ষার হার, জীবনযাপনের অবস্থা, শিশুমৃত্যুর নিম্নহার, অর্থনৈতিক সাম্যাবস্থা, লিঙ্গ সাম্যাবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা, দুর্নীতির নিম্নহার, পরিবেশ সচেতনতা, গরিব দেশকে সাহায্য সবদিক দিয়েই ডেনমার্ক ও সুইডেন অন্যান্য সকল দেশকে ছাড়িয়ে সবচেয়ে উপরে। তবে পাঠকদের আমরা এই বলে বিভ্রান্ত করতে চাই না যে, এইসব দেশে কোনো ধরনের সমস্যাই নেই। অবশ্যই তাদেরও সমস্যা আছে। তবে সেই সমস্যা সমাধানের জন্য তারা যৌক্তিক পথ। বেঁছে নেয়, উপর থেকে কারও সাহায্যের অপেক্ষা করে না, কিংবা হাজার বছর পুরনো গ্রন্থ ঘেঁটে সময় নষ্ট করে না।
যাই হোক, ইউরোপের ক্রমশ ধর্মহীনতার দিকে গমনের হার অসীম সময় পর্যন্ত চলবে না। ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডনের রাজনীতি ও সমাজনীতির গবেষক এরিক কফম্যান ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর জন্মহার পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন ধর্মহীনতার দিকে এই দেশগুলোর গমন চলবে মোটামুটি ২০৫০ পর্যন্ত, তারপর এটা আবার ঘুরে দাঁড়াবে এবং ২১০০ সালের মধ্যে আবার বর্তমান অবস্থায় ফিরে আসবে[৩৪৪]। তবে। একটা বিষয় নিশ্চিত যে, নাস্তিকতার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে মূলত দুটি বিষয়ের ওপর : শিক্ষা এবং অর্থনীতি। যদি বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জ্বালানী সমস্যা সঠিকভাবে সমাধান করা না হয় এবং যদি বর্তমান বিশ্বের ধনী দেশগুলো এই কারণে গরিব দেশের কাতারে নেমে আসে, যদি তাদের শিক্ষার হার নিম্নগামী হয়, তাহলে রাষ্ট্র হতে প্রথম যে জিনিসটি চলে যাবে তা হলো, নাস্তিকতা। কিন্তু আমরা যদি ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে এই সমস্যাগুলোর যৌক্তিক এবং বৈজ্ঞানিক সমাধান দিতে সক্ষম হই, যদি অধিকাংশের জন্য একটি সুন্দর জীবনের নিশ্চয়তা দান করতে পারি, নিশ্চয়তা দিতে পারি শিক্ষার আর তরুণ সমাজকে ক্রমশ উদ্দীপ্ত করতে পারি ইহজাগতিক বিজ্ঞানমনস্ক সংস্কৃতির প্রতি, তাহলে আর আমাদের অতিপ্রাকৃতিক কোনো স্রষ্টার দিকে মুখ করে থাকতে হবে না-যিনি আকাশ থেকে নেমে এসে সমাধান করে দিবেন, আমাদের সকল সমস্যা, দুঃখ-কষ্ট এবং গ্লানির।
.
বাংলাদেশে মুক্তবুদ্ধির চর্চা ও মুক্তমনার আত্মপ্রকাশ
বাংলাদেশে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির নাম সবাই কমবেশি জানেন। শহীদ জননী জাহানারা ইমাম এ সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা করেন ১৯৯২ সালের ১৯ জানুয়ারি। দীর্ঘদিন ধরে দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে জাহানারা ইমাম ১৯৯৪ সালের ২৬ জুন মৃত্যুবরণ করার পর থেকে বাংলাদেশে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি প্রতি বছরই জাহানারা ইমাম স্মৃতি পদক প্রদান করে থাকে। পদক থাকে দুটি। একটি দেওয়া হয় ব্যক্তিকে, আরেকটি দেওয়া হয় সংগঠনকে। ২০০৭ সালে জাহানারা ইমামের তেরোতম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত স্মারক সভায় ব্যক্তির জন্য বিবেচিত পদকটি পেয়েছেন মুক্তিযুদ্ধের উপ-প্রধান সেনাপতি এয়ার ভাইস মার্শাল একে খন্দকার। আর সংগঠনের পদকটি পেয়েছিল মুক্তমনা। পদকটি মুক্তমনার পক্ষ থেকে গ্রহণ করেন অধ্যাপক অজয় রায়া পদকের স্মারক পত্রে বলা হয়েছে–
বাংলাদেশে মৌলবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মুক্তচিন্তার আন্দোলনে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে ‘মুক্তমনা” ওয়েবসাইট। ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে দেশে ও বিদেশে কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে সেকুলার মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করণের পাশাপাশি তাদের বিজ্ঞানমনস্ক করবার ক্ষেত্রে ‘মুক্তমনা ওয়েবসাইটের জগতে এক বিপ্লবের সূচনা করেছে। বাংলাদেশের বিশিষ্ট মানবাধিকার নেতা ও বিজ্ঞানী অধ্যাপক অজয় রায়ের নেতৃত্বে বিভিন্ন দেশের তরুণ মানবাধিকার কর্মীরা এই ওয়েবসাইটকে তাদের লেখা ও তথ্যের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করছেন। ২০০১ সালে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের। ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যে নজিরবিহীন সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের শিকার হয়েছিল ‘মুক্তমনা’ তখন নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জনমত সংগঠনের পাশাপাশি আর্ত মানুষের সেবায় এগিয়ে এসেছিল। বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এবং ধর্ম-বর্ণ-বিত্ত নির্বিশেষে মানুষের সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিশেষ অবদানের জন্য ‘মুক্তমনা ওযেবসাইটকে ‘জাহানারা ইমাম স্মৃতিপদক ২০০৭’ প্রদান করা হলো।
বাংলাদেশে এর আগে কোনো ওয়েবসাইট জাহানারা ইমাম পদক পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে নি। স্মারকপত্রের প্রথম লাইনটি গুরুত্বপূর্ণ। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি এবারের পদক প্রাপ্তির বিবেচনায় মৌলবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতা বিরোধিতার পাশাপাশি মুক্তচিন্তার আন্দোলন’কেও গুরুত্ব দিয়েছে।
তাহলে স্বভাবতই প্রশ্নটি এসে পডে-এই মুক্তচিন্তার আন্দোলনটি কী, কেন এটি অনন্য কিংবা নিজগুণে স্বকীয়? যে সমাজ আর সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী আমরা, তার সবটুকুই যে নির্ভেজাল তা বলা যায় না। এতে যেমন প্রগতিশীল বস্তুবাদী উপাদান রয়েছে, তেমনই রয়েছে আধ্যাত্মবাদ, বুজরুকি, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস আর অপবিশ্বাসের রমরমা রাজত্ব; রয়েছে অমানিশার ঘোর অন্ধকার। এই অন্ধকার সুদীর্ঘকাল ধরে বংশ পরম্পরায় আমাদের চিন্তা চেতনাকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে এই চেতনার দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আসা সহজ নয় বরং বাস্তবিকই কঠিন ব্যাপার। রাহুল সাংকৃত্যায়ন একবার তার একটি লেখায় বলেছিলেন–
মানুষ জেলে যাওয়া বা ফাঁসির মঞ্চে ওঠাকে বিরাট হিম্মত মনে করে। সমাজের গোঁড়ামিকে ভেঙে তাদের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা, জেলে যাওয়া বা ফাঁসির মঞ্চে ওঠার চেয়ে ঢের বেশি সাহসের কাজ।
কথাটি মিথ্যে নয়। তাই ইতিহাসের পরিক্রমায় দেখা যায়, খুব কম মানুষই পারে আজন্ম লালিত ধ্যান ধারণাকে পরিত্যাগ করে স্বচ্ছভাবে চিন্তা করতে, খুব কম মানুষই পারে স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। খুব কম মানুষের মধ্যে থেকেই শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসে একজন আরজ আলী মাতুব্বর, প্রবীর ঘোষ, হুমায়ুন আজাদ কিংবা আহমেদ শরীফ। আমাদের শাসক আর শোষকশ্রেণি আর তাদের নিয়ন্ত্রিত বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা কথনোই চায় না জনগণ প্রথা ভাঙুক, কুসংস্কারের পর্দা সরিযে বুঝতে শিখুক, জানতে শিখুক অজ্ঞতা, শোষণ আর অসাম্যের মূল উৎসগুলো কোথায়। জনগণের জ্ঞান চক্ষু খুলে গেলেই তো বিপদ, তাই না! আর সেজন্যই জনগণকে অন্ধকারে রাখতে চলে বিজ্ঞানের মোড়কে পুরে ধর্মকে পরিবেশন, লাগাতার আধ্যাত্মবাণী প্রচারণা, পত্র পত্রিকায় বড় আকারে রাশিফল, সর্পরাজ এবং আধ্যাত্মবাদী গুরু আর কামেল পীরের বিজ্ঞাপন, মন্ত্রী আর নেতা-নেত্রীদের মাজার আর দরগায় সিন্নি দেওয়া অথবা নির্বাচন উপলক্ষে হজে যাওয়া, মাথায় কালো পটি বাঁধা। মুক্তমনাদের লড়াই এই সামগ্রিক অসতোর বিরুদ্ধে, অন্ধবিশ্বাস আর অপবিশ্বাসকে উস্কে দেওয়া এই সমাজ কাঠামোর বিরুদ্ধে। এ লড়াই বৌদ্ধিক, এ লড়াই সাংস্কৃতিক। এ লড়াই সমাজকে প্রগতিমুখী করার ব্রত নিয়ে সামগ্রিক অবক্ষয় আর অন্ধকার ভেদ করে আশার আলো প্রজ্বলিত করবার লড়াই। এ লড়াই আক্ষরিক অর্থেই আমাদের কাছে চেতনামুক্তির লড়াই।
চিন্তার এ দাসত্ব থেকে মুক্ত করার লড়াইযের ময়দানটি একদিনে গড়ে উঠে নি। আজ ইন্টারনেটের কল্যাণে বিশ্বাস এবং যুক্তির সরাসরি সংঘাতের ভিত্তিতে যে সামাজিক আন্দোলন বিভিন্ন ব্লগ কিংবা ফোরামগুলোতে ধীরে ধীরে দানা বাঁধছে, তা আমরা মনে করি প্রাচীনকালের ব্রাহ্মণ-চার্বাকদের লড়াইযেরই একটি বর্ধিত, অগ্রসর ও প্রায়োগিক রূপ। এ এক অভিনব সাংস্কৃতিক আন্দোলন, বাঙালির এক নবজাগরণ যেন। এ নবজাগরণকে রূপ দিতেই আবির্ভাব হয়েছিল মুক্তমনার, প্রথমে ফোরাম হিসেবে, পরে রূপ নিয়েছিল সামগ্রিক একটি ওযেব এবং পরবর্তীকালে ব্লগসাইটে। এর পরের কাহিনি তো ইতিহাস। মুক্তমনার অবদান যে কোথায় পৌঁছে গেছে তার উল্লেখ মেলে জাহানারা ইমাম পদকের স্মারক লিপিতে-’দেশে ও বিদেশে তরুণ প্রজন্মকে সেকুলার মানবিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করণের পাশাপাশি তাদের বিজ্ঞানমনস্ক করার ক্ষেত্রে মুক্তমনা ওয়েবসাইটের জগতে এক বিপ্লবের সূচনা করেছে।
মুক্তমনার আত্মপ্রকাশের ইতিহাসটি ছোট করে জেনে নেওয়া যাক। আরজ আলী মাতুব্বরের দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে ২০০১ সালে প্রশ্ন আর তর্ক-বিতর্কের মাধ্যমে জ্ঞানার্জনের প্রচেষ্টা এবং ধর্মান্ধতা আর মৌলবাদের বিরুদ্ধে মুক্তমনার প্রাথমিক লড়াই সূচিত হলেও পাশাপাশি পৃথিবী জুড়ে নির্যাতিত, নিপীড়িত মুক্তচিন্তাবিদদের সহযোগী মানবতাবাদী সংগঠন হিসেবে কাজ করার সচেতন প্রয়াস নেওয়া হয়। আসলে মানবিক দিকটি শুরু থেকেই মুক্তমনা কখনোই অগ্রাহ্য করে নি। আমরা খবর পাই পাকিস্তানে ইউনুস শাযিথ নামের এক চিকিৎসক ব্লাসফেমি আইনের শিকার হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন। তার অপরাধ, তিনি শ্রেণীকক্ষে লেকচার দিতে গিয়ে নাকি ছাত্রদের বলেছেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ তার নবুওত প্রাপ্তির আগ পর্যন্ত মুসলিম ছিলেন না। পাকিস্তানের মতো ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোতে ধর্ম এবং ধর্মপ্রচারক সম্পর্কে সামান্য বিপরীত কথাবার্তা সহ্য করা হয় না। শাস্তি একটাই, মৃত্যুদণ্ড। ইউনুস শায়িখ বন্দি হলেন এবং যথারীতি কারাগারে মৃত্যুর প্রহর গুনছিলেন। মুক্তমনা এই হতভাগ্য ব্যক্তির পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল। আমরা পিটিশন আর প্রতিবাদলিপির বন্যায় পাকিস্তান সরকারের মেইলবক্স একেবারে ভর্তি করে ফেললাম। আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালো আই. এইচ.ই.ইউ এবং জার্নালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল। আর অন্যদিকে ঢাকাতে ইউনুস শাযিথের মুক্তি এবং ব্লাসফেমি আইন বিলোপের দাবিতে দাবিতে প্ল্যাকার্ড, পোস্টার হাতে বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করলেন ড. অজয় রায়ের নেতৃত্বে অন্যান্য মুক্তমনা সদস্যরা। মুক্তমনার শুভানুধ্যায়ী এবং হোস্ট ড. অ্যালেন লেভিন চারিদিকে নেটওয়ার্ক তৈরি করে মানবতাবাদী সংগঠনগুলোকে উদ্বুদ্ধ ও এক ছাতার নিচে নিয়ে আসলেন। এমনিভাবে বিশ্বব্যাপী মানবতাবাদীদের প্রবল চাপে পাকিস্তান সরকার একসময় গোপনে ড. শাযিথকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, ড. শায়িখও সাথে সাথে দেশত্যাগ করলেন। ড. শায়িখ ক’দিন পরেই আমাদের সাথে যোগাযোগ করে মুক্তমনাকে তার পাশে থাকার জন্য কৃতজ্ঞতা জানালেন। এরপর তিনি মুক্তমনায় যোগদান করেন এবং বেশ ক’বছর ধরেই মুক্তমনায় লিখছেন।
ড. শায়িখের বিষয়টি মুক্তমনার প্রথম দিককার অন্যতম সফল কাজগুলোর একটি। এটি সফল হওয়ায় আমাদের উৎসাহ অনেক বেড়ে যায়। আমরা ইতোমধ্যেই বহু জায়গায় পিটিশন করেছি। আমিনা লাওয়াল নামের এক মহিলাকে শারিয়ার রজম’ থেকে বাঁচানোর জন্য মুক্তমনা উদ্যোগী হয় এবং শেষ পর্যন্ত সফলও হয়। তারপর থেকে মুক্তমনা আন্তর্জাতিকভাবে নানা ধরনের পিটিশন করেছে, আবেদন করেছে, কখনও প্যালেস্টাইনে নির্বিচারে গণহত্যা বন্ধের দাবিতে, কথনও গুজরাতে গণহত্যার বিচারের দাবিতে, কখনোবা উপমহাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষায, কথনও আওয়ামী লীগের জনসভায় বোমা হামলার নিন্দা করে, কখনও ভারতে নদী সংযোগ প্রকল্পের বিরোধিতা করে, কখনও তথাকথিত ‘বাংলা ভাই কে গ্রেফতারের দাবিতে, কখনোবা কানসাটে গণহত্যা বন্ধের দাবিতে।
বিগত ২০০১ সালের নির্বাচনের পর বিএনপি জামাত জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে-যখন সংখ্যালঘুদের ওপর নির্বিচারে অত্যাচার নিপীড়ন শুরু হলো, তখন এর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিকভাবে সচেতনতা তৈরি করতে শুরু করেছিল এই মুক্তমনাই। আসলে শুধু ‘অত্যাচার’ আর ‘নিপীড়ন’ বললে বোধহয় ভয়াবহতার মাত্রাটা বোঝা যাবে না। নির্বাচনের পরবর্তী কয়েক মাসে ঠিক কী হয়েছিল, তা বোঝা যাবে গার্ডিয়ানে প্রকাশিত জন ভাইদালের ‘Rape and torture empties the villages’ (জুলাই ২১, ২০০৩) একটি প্রবন্ধ পড়ে নিলেই। প্রবন্ধটিতে অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে পূর্ণিমা রানীর মতো হতভাগ্যদের ওপর সেসময় কীভাবে গণধর্ষণের স্টিমরোলার চালানো হয়েছিল। শুধু পূর্ণিমা রানীই একমাত্র শিকার নন, ভাইদালের মতে নির্বাচনোত্তর তিন মাসে ৬জনকে ডজন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, অন্তত এক হাজার নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছে আর কয়েক হাজার লোকের জমিজমা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। এধরনের রিপোর্ট শুধু গার্ডিয়ানে বা হিন্দুস্থান টাইমসে নয়, পাশাপাশি প্রকাশিত হয়েছিল ডেইলি স্টার, প্রথম আলো, সংবাদ, জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজসহ দেশের সকল শীর্ষস্থানীয় পত্রিকাগুলোতে। এমনকি মৌলবাদী আর সরকার সমর্থিত পত্রিকা ইনকিলাব আর সংগ্রামও একেবারে বাদ যায় নি। মুক্তমনার ঢাকা নিবাসী সদস্যরা ‘নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটির ব্যানারে ভোলা জেলায় অন্নদাপ্রসাদ নামের একটি গ্রামে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েছিল। তবে পর্যবেক্ষণই শুধু উদ্দেশ্য ছিল না, সেইসাথে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছিল যারা সাম্প্রদায়িক নিপীড়নের শিকার হয়েছে তাদের আর্থিক ও মানসিকভাবে সহায়তা প্রদান করা। আমরা দৃষ্টিপাত নামের একটি সংগঠনের সাথে মিলে অন্নদাপ্রসাদ গ্রামের দশটি পরিবারকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে সম্মত হই। সরকার পক্ষ থেকে আমাদের কাজকর্মকে ভালো চোখে দেখা হলো না। বক্তব্য দেওয়া হলো এই বলে যে, দেশের বাইরে এক বাংলাদেশ বিরোধী কুচক্রী মহল’ দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন থাকার পরামর্শ দিয়ে বেশ কিছু জ্বালাময়ী ভাষণও দিলেন। রটিয়ে দেওয়া হলো যারা দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার অপচেষ্টায় লিপ্ত আছে তারা হয় ভারতের ‘র’-এর এজেন্ট, নয়ত ইহুদিদের ‘মোসাদ’-এর আর নাহয় আমেরিকার সি.আই.এর! সেসময় অভিজিৎ রায় মুক্তমনায় ‘যুক্তির আলোয় দেশের ভাবমূর্তি এবং দেশপ্রেম’ নামের একটি প্রবন্ধ লেখেন, বাংলায়। সে প্রবন্ধে তিনি তুলে ধরেছিলেন দেশপ্রেমের যৌক্তিক সংজ্ঞা। তিনি বলেছিলেন, দেশ মানে দেশের মাটি নয়, দেশপ্রেম মানে কখনোই দেশের মাটির প্রতি বা প্রাণহীন নদীনালা আর পাহাড়-পর্বতের জন্য ভালোবাসা হতে পারে না। দেশপ্রেম মানে হওয়া উচিত দেশের মানুষের প্রতি প্রেম; লাঞ্ছিত, বঞ্চিত অবহেলিত গণ-মানুষের প্রতি ভালোবাসা। রাষ্ট্রের একটি প্রধানতম উপাদান হলো জনসমষ্টি। এই জনসমষ্টিকে বাদ দিয়ে শুধু কতকগুলো প্রাণহীন নদীনালা, খাল-বিল, পাহাড়-পর্বত আর মাটির প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টিকে আর যা-ই বলা হোক, দেশপ্রেম’ বলে অভিহিত করার কোনো যৌক্তিকতা নেই। উদ্ধৃতি হাজির করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের, আইনস্টাইনের আর হাল আমলের যুক্তিবাদী প্রবীর ঘোষের; দেখিয়েছিলেন ‘সনাতন দেশপ্রেম’ও শেষ পর্যন্ত কিন্তু একটা ডগমাই। মুক্তমনার অন্যান্য সদস্যরাও এ নিয়ে বিস্তর লেখালেখি করেছেন। দেশপ্রেম নিয়ে মুক্তমনাদের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সেসময় সচেতন মানুষ ধীরে ধীরে বুঝতে পেরেছিলেন, কোনো সরকারের অন্ধ আনুগত্যই দেশপ্রেম নয়। দেশে অরাজকতা, হত্যা নিপীড়নের কাহিনি যেকোনো মূল্যে কার্পেটের নিচে পুরে রেখে দেশকে আকাশে তুলে রাখার নামই দেশপ্রেম নয়, বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দেশের মানুষের বিবেক জাগিয়ে তোলাটাও দেশপ্রেমের অংশ। সংকীর্ণ দেশপ্রেমের সংজ্ঞা থেকে বেরিয়ে এসে যুক্তিবাদী দৃষ্টি দিয়ে দেশের ভাবমূর্তি’ দেখবার এই মানসিকতার উত্তরণ একদিনে হয় নি। এর কৃতিত্ব মুক্তমনারা দাবি করতেই পারেন।
মুক্তমনার সবচাইতে বড় অবদান সম্ভবত ইন্টারনেটে (এবং পরবর্তীকালে প্রিন্টেড মিডিয়ায়) বিজ্ঞানমনস্কতার প্রচার প্রসার। অভিজিৎ রায়ের ‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী’ সে উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছিল, পরে এটি বই হিসেবে বেরোয় ২০০৫ সালে। বন্যা আহমেদের ‘বিবর্তনের পথ ধরে সিরিজটিও বই হিসেবে বেরিয়েছে (২০০৭), সেইসাথে বেরিয়েছে ‘মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে (২০০৭)। এছাড়া আরও বেরিযেছে ‘স্বতন্ত্র ভাবনা : মুক্তচিন্তা ও বুদ্ধির মুক্তি’ (২০০৮), এবং ‘সমকামিতা : বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ-মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান (২০১০), পার্থিব (২০১১), মানুষিকতা (২০১৩)। প্রতিটি গ্রন্থের উদ্দেশ্য একই। বিজ্ঞানমনস্কতার প্রচার ও প্রসার। বিজ্ঞানমনস্কতা প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে লিখছেন ফরিদ আহমেদ, শাফায়েত, সিদ্ধার্থ, অপার্থিব, মেহুল কামদার, মীজান রহমান, অনন্ত, তানবীরা, জাহেদ আহমেদ, জাফর উল্লাহ, অজ্য রায়, বিপ্লব পাল, প্রদীপ দেব, আবুল কাশেম, আকাশ মালিক, শিক্ষানবিস, রৌরব, তানভীরুল, পৃথিবী, ইরতিশাদ আহমদ, সংশপ্তক, স্নিগ্ধা, আসিফ মহীউদ্দিন, হোরাস, টেকি সাফি, শফিউল জ্য, সৈকত চৌধুরী, আল্লামালাইনা, রূপম, তামান্না ঝুমু, নিলয়, লীনা রহমানসহ আরও অনেকেই। এ লেখকদের থেকেই উঠে এসেছে ‘যুক্তি’র মতো ম্যাগাজিন, নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে ‘মুক্তান্বেষা’ এবং ‘মহাবৃত্ত’। এই ‘বিজ্ঞানমনস্কতা’ ব্যাপারটি আমাদের কাছে সবসময়ই ভিন্ন অর্থ বহন করে। ‘বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার’ বলতে আমরা এটি বোঝাই না যে গ্রামে-গঞ্জে বিদ্যুৎ পৌঁছিয়ে দেওয়া কিংবা উন্নতমানের বীজ সরবরাহ করা। ওগুলোর প্রয়োজন আছে কিন্তু তা করার জন্য রাষ্ট্র এবং সরকারই আছেন। আমরা বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার বলতে বোঝাই কুসংস্কারমুক্ত, প্রগতিশীল ও বিজ্ঞানমুখী সমাজ গড়ার আন্দোলন। ঢাকা কলেজের প্রিয় শিক্ষক এবং বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের পরিচালক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের ভাষায় আমাদের আন্দোলন হচ্ছে ‘আলোকিত মানুষ গড়ার আন্দোলন। বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করলেই সে ‘বিজ্ঞানমনস্ক হয় না, হয় না আলোকিত মানুষ। তাই দেখা যায় এ যুগের অনেকেই বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেও বা বিজ্ঞানের কোনো বিভাগকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেও মনে-প্রাণে বিজ্ঞানী হতে পারেন নি, পারেন নি মন থেকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করতে বাংলাদেশের এক বিখ্যাত ইসলামি পদার্থ বিজ্ঞানী’ আছেন যিনি একবিংশ শতাব্দীতে এসেও শতাব্দী প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের মধ্যে ‘আধুনিক বিজ্ঞানের সন্ধান পান, মহানবীর মিরাজকে ‘আইনস্টাইনের থিওরি অব রিলেটিভিটি’ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চান। ভারতের এক স্বনামধন্য বিজ্ঞানী আবার বেদ আর গীতার মধ্যে ‘বিগব্যাং’ আর ‘টাইম-ডায়ালেশন’ খুঁজে পান। এরা বিজ্ঞান নিয়ে পড়েছেন ঠিকই, চাকরি ক্ষেত্রে সফলতাও হয়ত পেয়েছেন, কিন্তু মনের কোণে আবদ্ধ করে রেখেছেন সেই আজন্ম লালিত সংস্কারগুলো, আঁকড়ে ধরে রেখেছেন যুক্তিহীন ধর্মীয় ধ্যানধারণা। এই ‘বিজ্ঞানী’ তকমাধারী কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলোই বাংলাদেশে বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসারে সবচেয়ে বড় বাধা। বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ ডিগ্রিধারী ‘বিজ্ঞানী’ নামধারী মানুষগুলোর কুসংস্কারের সাথে যেমন আমরা পরিচিত হয়েছি, ঠিক তেমনই আমাদের দেশে আরজ আলী মাতুব্বর বা রঞ্জিত বাওয়ালীর মতো স্বল্পশিক্ষিত, ডিগ্রিহীন, সংস্কারমুক্ত ও যুক্তিবাদী মানসিকতার নির্লোভ মানুষও আমরা দেখেছি। এরাই আমাদের শক্তি।
মুক্তমনাদের বিরুদ্ধে কারো কারো একটি অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় যে, মুক্তমনারা দেশের মানুষের জন্য খুব বেশি কিছু করে না, যতটা না ঈশ্বর, আধ্যাত্মিকতার বিরোধিতা কিংবা ডারউইন দিবস উদ্যাপনে ব্যয় করে। এ ধরনের অভিযোগ যারা করেন তারা ভুলে যান এ ক’বছরে মুক্তমনাদের সফল প্রোজেক্টগুলোর কথা। হ্যাঁ, মুক্তমনা ঘটা করে ডারউইন ডে, হিউম্যানিস্ট ডে, র্যাশনালিস্ট ডে, আর্থ ডে ইত্যাদি পালন করেছে ঠিকই, কিন্তু যখন প্রয়োজন হয়েছে দেশের মানুষের প্রয়োজনে মুক্তমনা সচেতনভাবেই এগিয়ে এসেছে। অধ্যাপক অজয় রায় সেকথাগুলোই শুনিয়েছেন অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় জাহানারা ইমাম স্মারক সেমিনারে :[৩৪৫]
আমরা শুধু ধর্মান্ধতা আর মৌলবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি শোনাই না, আমরা মানবতার সপক্ষে লড়াইয়ে নামি–
১. ব্লাসফেমির বিরুদ্ধে মানবতাকে বাঁচাতে পাকিস্তানের কারাদণ্ড প্রাপ্ত ফ্রিথিষ্কার ড. ইউনুস শাইখকে বাঁচাতে বিশ্বময় আন্দোলন গড়ে তুলি। আমাদের সক্রিয় সহযোগী ছিল ‘IHEU, Rationalist International, Amnesty International, Dhaka Rationalist and Secularist Union এবং ঢাকার মুক্তমনাদের Save Dr. Yunus Shaikh Committee’, যারা রাস্তায় নেমে দিনের পর দিন আন্দোলন, মিটিং, মিছিল, সেমিনার, পথসভা ও পাকিস্তানি দূতাবাসের সামনে প্রেসিডেন্ট মোশাররফের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছিলেন কবির চৌধুরী, বিচারপতি আবদুস সোবহানসহ দেশের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী ও প্রগতির পক্ষের মানুষ। আমাদের সাফল্য এসেছিল। পাকিস্তান সরকার তাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। বর্তমানে তিনি যুক্তরাজ্যে রয়েছেন এবং আমাদের একজন সক্রিয় সদস্য।
২. আমরা আন্দোলন গড়ে তুলি শাহরিয়ার কবিরের পক্ষে তার মুক্তির লক্ষ্যে, যখন খালেদা নিজামী সরকার তাঁকে বিমান বন্দরে গ্রেপ্তার করে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে। আমরা সফল হই তাকে মুক্ত করতে দেশে বিদেশে গড়ে ওঠা সফল আন্দোলনের গড়ে তোলার মাধ্যমে।
৩. পরে দ্বিতীয়বার শাহরিয়ার কবির, মুনতাসীর মামুন ও সাংবাদিকসহ অনেক অবরুদ্ধ অত্যাচারিত ব্যক্তিদের পক্ষে মানবতার মুক্তির পক্ষে আন্দোলনে নামি এবং এখানেও আমরা সফল হই।
৪. আমরা এককভাবে প্রশিকার পক্ষে’ নেটওয়ার্কে আন্দোলন গড়ে তুলি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সহযোগিতায়। প্রশিকা মহাপরিচালককে মুক্তি দিতে বাধ্য হন সরকার।
৫. আমরা সাম্প্রদায়িকতার নগ্ন প্রকাশ সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের বিরুদ্ধে সর্বদাই উচ্চকণ্ঠ : আমরা মৌলবাদীদের হাতে মুসলমান বা হিন্দু যে-ই নির্যাতিত হয়েছে তার পক্ষে দাঁড়িয়েছি, মৌলবাদী সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছি আমাদের সীমিত শক্তি নিয়ে। গুজরাটে আহমেদাবাদের জিঘাংসা বৃত্তিকে আমরা ধিক্কার জানিয়েছি। নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে তাকে অপসারণের দাবিতে আমরা ভারতীয় প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীকে স্মারকলিপি ও প্রতিবাদপত্র পাঠিযেছি, ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে একসাথে কাজ করেছি সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলতে।
৬. একইভাবে ২০০১ সালে খালেদা-নিজামীর লেলিয়ে দেওয়া সাম্প্রদায়িক শক্তি বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপর হত্যা, লুণ্ঠন, ঘরবাড়িতে অগ্নি সংযোগ, উপাসনালয় ধ্বংস ও অপবিত্রকরণের যে ঘৃণ্য নিদর্শন স্থাপন করেছে তার বিরুদ্ধে দেশের সেকুলার শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছি। মুক্তমনার প্রতিষ্ঠাতা উপদেষ্টা অধ্যাপক অজয় রায় অন্যান্য মুক্তমনা ও। বুদ্ধিজীবীদের সাথে নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী আন্দোলন ‘নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটির ব্যানারে। তারা গঠন করেছিলেন অধ্যাপক জিল্লুর রহমানের নেতৃত্বে ‘গণ তদন্ত কমিশন’, যার প্রতিবেদন প্রকাশিত হয় ২০০২-এর ডিসেম্বরে এবং তাৎক্ষণিক ভাবে আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়46। প্রবাসী মুক্তমনার সদস্যরা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে প্রতিবাদপত্র প্রেরণ করেন সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে চালিত নির্যাতন বন্ধের দাবিতে। তারা ঘৃণা প্রকাশ করেছেন মৌলবাদী শক্তিকে সরকার প্রশ্রয় দেওয়ায়।
৭. আমরা শুধু তাত্ত্বিক আন্দোলন করি না। আমরা আর্ত মানবতার পাশে পার্থিব ভাবেই এগিয়ে আসি। (ক) সাম্প্রদায়িক ভাবে নির্যাতিত ভোলার অন্নদাপ্রসাদ ও ফাতেমাবাদ গ্রামে ১০০টি পরিবারকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে এগিয়ে এসেছি ‘দৃষ্টিপাত’ নামক আমাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের পাশে। এই প্রকল্পে ১০০টি ঘরবাড়ি নির্মাণ, জমি ক্রয় করে দেওয়া, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার ব্যয় ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে আমরা সংশ্লিষ্ট ছিলাম। আমরা এসে দাঁড়িয়েছিলাম পূর্ণিমার পাশে, রিতার পাশে, মাধুরীর পাশে, রাজকুমার বাবুর পাশে, নরহরি কবিরাজের পাশে, জনের পাশে, সিতাংশু মরমুর পাশে, ফাতেমার পাশে, মিনতির পাশে- এরা সবাই নরপশুদের পাশবিক অত্যাচারের শিকার।
৮. আমরা সাংবাদিক মানিক সাহার পরিবারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, তার দুটি কন্যার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছি। সাংবাদিক বিভুরঞ্জনের পাশে দাঁড়িয়েছি।
৯. দুর্ঘটনা কবলিত মানবতাবাদী শাহরিয়ার কবির, কাজী মুকুল ও তাদের সহকর্মীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছি যৎসামান্য শক্তি নিয়ে, আমরা ইসলামি মৌলবাদের শিকার হুমায়ুন আজাদের অসহায় পরিবারের প্রতি সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছি। হুমায়ুন আজাদ ফাউন্ডেশন গড়ে তুলতে সাধ্যমতো সহায়তা করেছি।
১০. ব্রহ্মপুত্রের চরে বন্যাবিধ্বস্ত একটি নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল আমরা পুনর্নির্মাণ করেছি এবং আমরা এর পরিচালনার দায়ভার গ্রহণ করেছি। সেখানে মুক্তিযুদ্ধের শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তোলার প্রকল্প গ্রহণ করেছি এবং সে উপলক্ষে কয়েক হাজার স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধার সম্মেলন করেছি এবং স্মৃতিস্তম্ভের শিলান্যাস করেছি।
১১. চোলেশ মিছিলের মৃত্যুর বিচার চেয়ে পিটিশন করেছি, তার পরিবারকে আর্থিকভাবে যথাসম্ভব সাহায্য করেছি।
১২. আমরা পিটিশন করেছি, বক্তব্য রেখেছি কিংবা জনসংযোগ করেছি ভারতে অবৈধ নদী সংযোগের প্রতিবাদে, গুজরাটে মুসলিম জনগণকে নির্বিচারে হত্যার প্রতিবাদে, কানসাটে নিষ্ঠুরভাবে কৃষক-বিদ্রোহ দমনের প্রতিবাদে, জাফর ইকবাল এবং হাসান আজিজুল হককে সাম্প্রদায়িক মহল থেকে মৃত্যু-হুঁমকি দেওয়ার প্রতিবাদে, সি.আর.পি-এর প্রতিষ্ঠাতা ভ্যালেরি টেলরের অপসারণের প্রতিবাদে, কিংবা সালমান রুশদি অথবা তসলিমা নাসরিনের ওপর ফতোয়ার প্রতিবাদে।
এগুলো কি দেশের মানুষের জন্য করা নয়? আত্মপ্রচারণার সুর ধ্বনিত হলেও, আমরা বিনীতভাবেই বলতে চাই মুক্তমনা উপরের সবগুলো কাজই সাফল্যের সাথে করেছে। অতি সম্প্রতি আমরা অসুস্থ প্রবীণ রাজনীতিবিদ এবং সাংবাদিক নির্মল সেনের চিকিৎসার জন্য যথাসম্ভব সাহায্য করেছি[৩৪৭]। সাহায্য করেছি কার্টুনিস্ট আরিফের মায়ের চিকিৎসার জন্যও[৩৪৮]। তারপরও একটি বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। যারা যুক্তিবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষের চেতনামুক্তি আর সেই পথ ধরে শোষণমুক্তির স্বপ্ন দেখেন তাদের কিন্তু একটা বিষয়ে সচেতন থাকতেই হবে। উপলক্ষ যেন লক্ষ্যকে ছাড়িয়ে না যায়। কুসংস্কার মুক্তির লক্ষ্যে পৌঁছুতে জনকল্যাণমূলক কাজকর্ম কেবল উপলক্ষই হতে পারে, এ বিষয়ে অতি সচেতনতার প্রযোজনা স্পষ্ট মনে রাখতে হবে এই সত্যটি-জনসেবা করে আর যা ই করা যাক, সমাজব্যবস্থা পাল্টানো যায় না, সার্বিক শোষণ মুক্তি ঘটতে পারে না। শোষণ মুক্তি ঘটতে পারে শুধু সাধারণ মানুষের সচেতনতাবোধ থেকে। সচেতনতাবোধ যেন তৈরি না হয় সে জন্য শোষিতের ক্ষোভ ভুলিয়ে রাখে শাসকশ্রেণী। গরিবের ক্ষোভ ভুলিয়ে রাখতে ধনীর অর্থে চলে ‘দরিদ্র নারায়ণ সেবা।’ দরিদ্র-নারায়ণের সেবাই যাদের কেবল লক্ষ্য তারা আসলে কখনোই চায় না সমাজ থেকে দারিদ্র্য দূর হোক, কেন না দারিদ্র্য দূর নয়, বরং দারিদ্র্যকে পুঁজি করে জনগণের ‘মগজ ধোলাই’ই তাদের অন্যতম লক্ষ্য। এধরনের সেবামূলক কাজে দুয়েকটি দরিদ্রের তাৎক্ষণিক লাভ হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ দারিদ্র্যক্লিষ্ট মানুষের জন্য পড়ে থাকে অনন্ত বঞ্চনাময় জীবন। অর্থনৈতিকভাবে দেশকে স্বাবলম্বী করার চাইতে মগজ ধোলাই করে জনচিত্ত জ্য করার পদ্ধতিটি সফলভাবে কাজে লাগায় বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। সেজন্যই মাদার তেরেসা, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবা সংঘ, তবলীগ জামাত ইত্যাদি নানা সংগঠন নানা কৌশলে জনকল্যাণমূলক কাজের সাথে নিজেদের জড়িত রেখেছে। গড়ে উঠেছে ইসলামি এনজিও কৌশলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ঠিকমতো দান খয়রাত করলে, জাকাত দিলে দারিদ্র নাকি সমাজ থেকে এমনিতেই দূর হয়ে যাবে। কিন্তু ইতিহাস বলে অন্য কথা। এ ধরনের দান খয়রাত, জাকাত আর সমাজসেবার মাধ্যমে সমাজের শোষণ মুক্তি ঘটেছে এমন একটি দৃষ্টান্তও ইতিহাসে নেই। হাজারটা রামকৃষ্ণ মিশন, সেবা সংঘ, তবলীগ জামাত, হাজারটা মাদার তেরেসা, হাজী মুহাম্মদ মহসিন বাংলাদেশের কিংবা ভারতের জনতার শোষণ মুক্তি ঘটাতে পারবে না। আমরা সমাজসেবার বিরুদ্ধে নই, কিন্তু ‘উদ্দেশ্যমূলক’ জনসেবার মাধ্যমে মগজ ধোলাই করে মানুষকে অন্ধ রাখার অভিসন্ধির বিরুদ্ধে।
মুক্তমনাদের বিরুদ্ধে আরেকটা অভিযোগ মুক্তবুদ্ধি, নাস্তিক্যবাদ, মানবতাবাদ এগুলোর চর্চা করে তারা গণবিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন। এর জবাবে প্রবীর ঘোষের মতো বলা যায়, যেকোনো অসুস্থ সমাজে সুস্থ সচেতন, যুক্তিবাদী মানুষ বিচ্ছিন্ন হতে বাধ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে গ্যালিলিও, প্যারাসেলস, ব্রুনো, বিদ্যাসাগরসহ বহু চিন্তাবিদের নাম উল্লেখ করা যায় যারা প্রত্যেকেই ছিলেন সমাজে একাকী। একাকী ছিলেন আরজ আলী মাতুব্বর বা আহমেদ শরীফও। কিন্তু এইসব বিদ্রোহী মানুষগুলো প্রথাগত স্থবিরতাকে চূর্ণ করতে গিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন, সেসময়কার বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে। সেকালের বিচ্ছিন্ন বিশাল ব্যক্তিত্বদের মূল্যায়ন করার ক্ষমতা ছিল না তৎকালীন মানবগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের এবং মগজ বেচা বুদ্ধিজীবী তকমাধারীদের। আজ সেসব বিচ্ছিন্ন মানুষেরাই হয়ে উঠেছেন এক একজন মহামানব, শ্রদ্ধা, আদর্শ ও প্রেরণার উৎস। যে বিচ্ছিন্নতার অর্থ পচনধরা, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজকে সংস্কারমুক্ত করা, যে বিচ্ছিন্নতার অর্থ শোষণের অবসানমুখী সংগ্রাম, যে বিচ্ছিন্নতার অর্থ মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক করে সুস্থ সংস্কৃতিতে ফিরিয়ে আনা, সে বিচ্ছিন্নতা অবশ্যই কাম্য। একটা সময় আমরা দেখেছি ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার অবসানের মধ্য দিয়ে বস্তুবাদের বিকাশ অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছিল। ইতিহাসের পরিক্রমায় আমরা একে একে দেখেছি ভারতীয় লোকায়ত বা চার্বাক দর্শন, গ্রিসের আযোনিয়ার বস্তুবাদী দর্শন, পশ্চিম এশিয়ার মুসলিমদের মোতাজিলা দর্শন, ইউরোপের দার্শনিকদের (বেকন, লক, হবস, হিউম প্রমুখ) ইহজাগতিক দর্শন, ফরাসি বিপ্লব, ইউরোপের রেনেসাঁ এবং উনিশ শতকে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিওদের কল্যাণে বাঙালিদের নবজাগরণ; আমরা সেই ঐতিহ্যের অনুসারী, জাতীয়ভাবে আমরা সহজিয়া, বাউলিয়ানার মতো বিভিন্ন অজ্ঞেয লোকজ মতবাদ, বিভিন্ন সমমনা ইহজাগতিক সংগঠন ও ব্যক্তির যুক্তিবাদী ভাবধারার উত্তরসূরি। ড. অজয় রায়ও ঠিক সেকথাই বলেছেন জাহানারা ইমাম স্মরণ সভায়–
আমরা বিংশ শতাব্দীর বাংলার উদারচেতা পুনর্জাগরণের উত্তরসূরি, ডিরোজিওর চিন্তা চেতনার অনুসারী, আমরা মনে করি শিখা গোষ্ঠীর ঐতিহ্যের ধারক ‘জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি যেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব’, আমরা আরজ আলী মাতুব্বরের আদর্শের সৈনিক, আমরা বেগম রোকেয়া, লীলা রায়, ফুলরেণু গুহের, সুফিয়া কামালের, জাহানারা ইমামের পথে চলতে প্রত্যয়দীপ্ত….।
সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, ধর্মান্ধতা, কূপমণ্ডুকতা আর সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানমনস্ক ও যুক্তিনিষ্ঠ এক প্রজন্ম গড়ে তোলার লক্ষ্যে জনগণের মধ্যে দুর্বার আন্দোলন গড়ে উঠেছে। আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি ভারতে প্রবীর ঘোষের নেতৃত্বে ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতি’ সেদেশের যুক্তিবাদী আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। তার সুযোগ্য নেতৃত্বেই ‘যুক্তিবাদী চিন্তা আজ সেখানে ব্যক্তিগণ্ডি অতিক্রম করে আন্দোলনের রূপ পেয়েছে। আন্দোলিত হয়েছে লক্ষ-কোটি মানুষ, আন্দোলিত হয়েছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, নাট্য সংস্থা, বিজ্ঞান ক্লাবসহ বহু সংগঠন; এরা অংশ নিয়েছে যুক্তিবাদী চিন্তার বাতাবরণ সৃষ্টিতে প্রত্যাশা বেড়েছে অনেক। তৈরি হয়েছে নতুন নতুন প্রতিশ্রুতিশীল লেখক। ইন্টারনেটে তৈরি হয়েছে বহু ব্লগ সাইট। আমাদের দেশে ‘বিজ্ঞান চেতনা পরিষদ’, ‘জনবিজ্ঞান আন্দোলন’, ‘মুক্তচিন্তা চর্চা কেন্দ্র’, ‘বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী কাউন্সিল, সিলেট’, ‘বাংলাদেশ যুক্তিবাদী সমিতি ইত্যাদি বিভিন্ন নামে সংগঠন গড়ে উঠেছে প্রায় একই উদ্দেশ্য সামনে রেখে। কুসংস্কার, ভাববাদ, আধ্যাত্মবাদ, নিয়তিবাদ ও অলৌকিকতা-মুক্ত এক আলোকিত বাঙালি প্রজন্ম গড়ে তুলতে অবদান রেখে চলেছে ‘মুক্তমনা। এদের কারণেই আজকে আমাদের এত বড় প্রাপ্তি। জাহানারা ইমাম স্মৃতি পদক প্রাপ্তির মতো বিরল সম্মান অর্জন। আমরা আর কোনো বাঙালি ওযেবসাইট বা ফোরামের খবর জানি না, যারা সাম্প্রতিক সময়ে এমন সম্মান অর্জন করে নিতে পেরেছে। মুক্তমনা আজ শুধু একটি ব্লগ সাইট নয়, এটি একটি সফল আন্দোলনের নাম। মুক্তমনা শব্দটির ব্যাপ্তি আজ এতই গভীরে, যে বিভিন্ন ফোরাম এবং ব্লগ সাইটে সমমনা প্রগতিশীল লেখকদের আজ ‘মুক্তমনা লেখক হিসেবে অভিহিত করা হয়।
.
নতুন দিনের নাস্তিকতা : নেতৃত্ব দিচ্ছেন ব্লগাররা
শুধু মুক্তমনাতেই নয়, আজকে যেকোনো বাংলা ব্লগে গেলেই মুক্তবুদ্ধির লেখা সমৃদ্ধ বহু প্রবন্ধ চোখে পড়ে। বহু লেখকই ধর্মকে ক্রিটিক্যালি দেখছেন এবং লিখেছেন। আজকে একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে তথ্য যেখানে মুক্ত, সেখানে সত্যিটা যাচাই করে নেওয়া অনেক সহজ। এই কিছুদিন আগেও তথ্যের অবাধ প্রবাহ যখন রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল তখন এইভাবে বিভিন্ন সাইটে এত বেশি মুক্তবুদ্ধির লেখা সমৃদ্ধ রচনা আমরা দেখি নি। ব্লগারদের উপর সাম্প্রতিক রাষ্টীয়। নিপীডন এবং নির্যাতন প্রমাণ করেছে যে তাদের শক্তিকে আর শাসক-যন্ত্রের পক্ষে খাটো করে দেখা সম্ভব হচ্ছে না।
শুধু ব্লগ কেন, পৃথিবীর দিকে তাকালে দেখা যাবে, বহু দেশেই বিশেষ করে ইউরোপের দেশগুলোতে লোকজন এখন ধর্মের ধারই ধারে না। চার্চগুলো খালিই পড়ে থাকে। অনেকেই মনে করেন, নাস্তিকতাকে ধর্ম হিসেবে দেখলে ‘ফাস্টেস্ট গ্রোয়িং রিলিজিয়ন সম্ভবত ধর্মহীনতার দিকেই রায় দিবে[৩৪৯]। ছোটবেলা থেকে মগজ ধোলাইয়ের মতো স্রেফ পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত ধর্ম বিশ্বাসটা মাথায় জোর করে ঢুকিয়ে না দিয়ে পরিণত বয়সে এসে ‘সবকিছু দেখে শুনে, যাচাই বাছাই করে’ ধর্মকে গ্রহণ করার সুযোগ দেওয়া হলে আমরা বহু ধার্মিককে নাস্তিক হিসেবে দেখতে পেতামও এটা সত্যিই বলা যায়।
আমাদের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা এবং মানবতা শিশুকাল অতিক্রম করে গেছে বহু আগেই। এখন আর আমরা রূপকথার কল্পিত পরম পিতা নিয়ে মোহিত নই, যে পরম পিতা ‘ডাবের ভিতর পানি কেন’ থেকে শুরু করে বিগব্যাং কিংবা ব্ল্যাকহোল পর্যন্ত সবকিছুর পেছনেই একমাত্র গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা হিসেবে হাজির হবেন আর আমাদের প্রযোজনের অলীক ত্রাণকর্তা হিসেবে নিজেকে পরিচিত করবেন। সময় এগিয়েছে অনেক, আমরা নিজেরাই এখন নিজেদের দায়িত্ব নিতে সম, মানুষ নিজেই আজ নিজের ভাগ্যবিধাতা। আমরা আর রূপকথার জাল বুনে নিজেদের প্রবোধ দিতে চাই না, বরং বিজ্ঞানের সাম্প্রতিক জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এখন জীবন সাজাতে চাই। অন্যদিকে ধর্মগুলো এখন প্রগতির অন্তরায়, বিজ্ঞানের অন্তরায়, নারীমুক্তির পথে প্রধান বাধা। ধর্মগুলো নৈতিকতার নামে পুরনো আমলের জিনিস শেখাতে চায়। মানুষের উদ্ভব সম্বন্ধে ভুল ধারণা দেয়, বিজ্ঞানের নানান অপব্যাখ্যা হাজির করে। আর জিহাদ, ধর্মযুদ্ধ, জাতিভেদ, নিম্ন বর্ণের ওপর অত্যাচার কিংবা নারীদের অন্তরিন রাখার বৈধতা এগুলো তো আছেই। এগুলোকে ‘না’ বলার মাধ্যমেই প্রগতিশীল সমাজ গঠন সম্ভব, সেই সাথে সম্ভব বিশ্বাসের ভাইরাসমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার দিকে এগিয়ে যাওয়ার। এটাই আজ সময়ের দাবি।
পরিশিষ্ট – অক্কামের ক্ষুর এবং বাহুল্যময় ঈশ্বর
অক্কামের ক্ষুরকে দর্শনশাস্ত্রে অনেক সময় মিতব্যয়িতার নীতি’ (Principle of Parsimony/Economy) কিংবা ‘সরলতার নীতি’ (Principle of Simplicity) হিসেবে অভিহিত করা হয়। সংক্ষেপে এর মূলনীতিটি হলো–
Pluralitas non est ponenda sine neccesitate (Plurality should not be posited without necessity).
বাংলা করলে দাঁড়ায়– ‘অনাবশ্যক বাহুল্য সর্বদাই বর্জনীয়।
এই নীতি প্রয়োগ কিন্তু বিজ্ঞানে, ধর্মে, দর্শনে খুবই ব্যাপক। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ‘অক্কামের ক্ষুরের প্রয়োগ হরহামেশাই লক্ষ্য করা যায়। বিজ্ঞানীরা অষ্কামের যে মূলনীতিটি অনুসরণ করেন তা হলো ‘যদি দুটি বৈজ্ঞানিক মডেল একই রকম ভবিষ্যদ্বাণী কিংবা ফলাফল প্রদান করে থাকে, তবে অপেক্ষাকৃত সহজ মডেলটি সমাধান হিসেবে গ্রহণ করো’ একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। একটা সময় গ্রহদের অনিয়ত-গতিপ্রকৃতি জ্যোতির্বিদদের কাছে বড় ধরনের তাত্ত্বিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। কেপলার এই সমস্যা সমাধান করতে আমাদের সামনে হাজির করেছিলেন তিনটি সূত্র। আর পরবর্তীকালে একই সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে কেপলারের এই তিনটি নিয়মের বদলে নিউটন আমাদের দিলেন একটি মাত্র সূত্র ‘মহাকর্ষীয় ব্যস্তবর্গীয় নিয়ম (Inverse Law of Gravity) যা দিয়ে গ্রহ উপগ্রহের চলাচলজনিত সমস্যাগুলোর একটা সহজ সমাধান পাওয়া যায়। দেখা গেল, এই একটি নিয়ম থেকেই কেপলারের পূর্বেকার নিয়মগুলো স্বতঃসিদ্ধভাবে বেরিয়ে আসে। কাজেই যখন থেকে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রটিকে ‘বৈজ্ঞানিক মডেল হিসেবে গ্রহণ করা হলো, কেপলারের সূত্রগুলো ‘অনর্থক বাহুল্য হিসেবে পরিত্যক্ত হলো সংগত কারণেই। এটি অক্কামের সূত্রের একটি খুবই সার্থক প্রয়োগ।
অক্কামের ক্ষুরের আরেকটি সার্থক প্রয়োগ দেখা যায় ইথারের ক্ষেত্রে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পদার্থ বিজ্ঞানীরা আলো চলাচলের জন্য মাধ্যম হিসেবে ইথার’ নামক একটি অদৃশ্য, ঘর্ষণহীন, রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় এবং ‘সর্বভূতে বিরাজমান’ এক রহস্যময় পদার্থ কল্পনা করেছিলেন। তাদের ধারণা ছিল শব্দ চলাচলের জন্য যেমন মাধ্যমের প্রয়োজন, তেমনই আলো চলাচলের জন্যও একটি মাধ্যম থাকতেই হবে। তারা ধরে নিয়েছিলেন এই পুরো মহাবিশ্বটাই ডুবে রয়েছে ইথার নামক এক অদৃশ্য পদার্থের অথৈ মহাসমুদ্রে। আর এই ইথার নামক মাধ্যমের সাহায্যেই আলো অনেকটা শব্দের মতোই তরঙ্গাকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ১৮৮০ সালে মাইকেলসন-মর্লির বিখ্যাত পরীক্ষা এবং তারও পরে ১৯০৫ সালে আলবার্ট আইনস্টাইনের আপেক্ষিক তত্ব’ তাত্ত্বিকভাবে ইথারের অস্তিত্বকে নস্যাৎ করে দিল। গন্ধহীন, স্পর্শহীন রহস্যময় ‘ইথার’ ‘অহেতুক বাহুল্য হিসেবে পরিত্যক্ত হলো।
অক্কামের ক্ষুরের ব্যাপকতর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় দর্শনেই। নাস্তিক্যবাদী দার্শনিকরা, অক্কামের ফুরের প্রযোগে যুক্তি দেখিয়ে থাকেন, ঈশ্বরের অনুমান নিতান্তই একটি অপ্রয়োজনীয় অনুকল্প। কীভাবে? নিম্নোক্ত দুটি হাইপোথিসিস বা অনুকল্প বিবেচনায় আনা যাক—
১) আমাদের সামনে এক জটিল মহাবিশ্বের অস্তিত্ব রয়েছে, যেটি প্রাকৃতিক নিয়মে (Natural Process) উদ্ভূত হয়েছে। অর্থাৎ,
০ মহাবিশ্বের অস্তিত্ব > প্রাকৃতিক নিয়ম
২) আমাদের সামনে এক জটিল মহাবিশ্বের অস্তিত্ব রয়েছে, এবং একজন ঈশ্বর’ও রয়েছেন যিনি এই মহাবিশ্ব তৈরি করেছেন। এখানে ‘ঈশ্বর স্বভাবতই একটি পৃথক সত্ত্বা হিসেবে দেখা দিচ্ছে। অর্থাৎ,
০ মহাবিশ্বের অস্তিত্ব > নিয়ম + ঈশ্বর
যদি এই দুইটি পথের মধ্যে একটিকে পছন্দ করতে হয়, তবে ‘অক্কামের সূত্র এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজটিকে সমাধান হিসেবে গ্রহণ করতে বলবে অর্থাৎ প্রথম সমাধানটি এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হিসেবে বিবেচিত হবে।
কেউ কেউ অবশ্য তৃতীয় একটি সমাধানকে অপেক্ষাকৃত সহজ হিসেবে বিবেচনা করতে পারেন–
আমাদের সামনে কোনো জটিল। মহাবিশ্বের অস্তিত্ব নেই আসলে সবই মাযা আমাদের কল্পনা!
তবে এই তৃতীয় সমাধানটি আমাদের সলিপসিজমের (Solipsism) পথে নিয়ে যায় যা অধিকাংশ যুক্তিবাদীর কাছে অগ্রহণযোগ্য।
জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অক্কামের সূরের চমৎকার একটি প্রয়োগ আমরা পাই যখন চার্লস ডারউইনের প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটা বিবর্তন তত্ত্ব উইলিয়াম প্যালের ‘ডিজাইন আর্গুমেন্ট’ বা সৃষ্টির পরিকল্পিত যুক্তিকে বাতিল করে দিয়েছিল। উইলিয়াম প্যালে (১৭৪৩ ১৮০৫) ‘র বিখ্যাত বই ‘Natural Theology, or Evidence of Existence and Attributes of the Deity, collected from the Appearences of Nature’–প্রকাশিত হয় ১৮০২ সালে। ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এটি গুরুত্বপূর্ণ একটি বই ছিল সেসময়। জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়েও প্যালে ভেবেছিলেন বিস্তর, কিন্তু নিজেই শেষ পর্যন্ত বলেছিলেন ‘বুদ্ধিদীপ্ত স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞান উপযুক্ত মাধ্যম নয়’; এ ক্ষেত্রে প্যালের ‘উপযুক্ত মাধ্যম মনে হয়েছিল বরং জীববিজ্ঞানকে। আর পূর্ববর্তী অন্যান্য ন্যাচারাল থিওলজিয়ানদের মতোই প্যালেও জীবজগতকে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে জীবের অভিযোজনের ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। প্যালে লক্ষ্য করেছিলেন যে, প্রতিটি জীবদেহে নির্দিষ্ট কাজ করবার জন্য নির্দিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রয়েছে, যা জীবটিকে নির্দিষ্ট কোনো পরিবেশে টিকে থাকতে সহায়তা করে। তিনি জটিল জীবদেহকে ঘড়ির কাঠামোর সাথে তুলনীয় মনে করেছিলেন, এবং তার মধ্যেই দেখেছিলেন স্রষ্টার সুমহান পরিকল্পনা, উদ্দেশ্য আর নিপুণ তুলির আঁচর। আর চোখকে প্যালে অনেকটা জৈব-টেলিস্কোপ হিসেবে ধরে নিয়েছিলেন। তাই খুব স্বাভাবিক ভাবেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, ঘড়ি কিংবা টেলিস্কোপ তৈরি করার জন্য যেহেতু একজন কারিগর দরকার, চোখ ‘সৃষ্টি করার জন্যও প্রয়োজন একজন অনুরূপ কোনো কারিগরের। সেই কারিগর যে একজন ব্যক্তি ঈশ্বর’ (Personal God) ই হতে হবে তা প্যালে খুব পরিষ্কার করেই বলেছিলেন তার গ্রন্থে।
প্যালের এই ‘ঘড়ির কারিগরের যুক্তি’ দর্শনশাস্ত্রে পরিচিত ‘পরিকল্পিত যুক্তি’ বা ‘আমেন্ট অব ডিজাইন নামে। এই যুক্তি ঈশ্বর নামক একটি সত্ত্বার অস্তিত্বের পেছনে অত্যন্ত জোরালো যুক্তি হিসেবে বিশ্বাসীরা ব্যবহার করতেন। ডারউইনের বিবর্তন তত্বই প্রথমবারের মতো এই ডিজাইন আর্গুমেন্টকে শক্তিশালীভাবে চ্যালেঞ্জ করে ভুল প্রমাণ করে দিয়েছিল। ডারউইন প্রস্তাব করলেন জীবদেহকে কেবল ঘড়ির সদৃশ যন্ত্রের মতো কিছু ভেবে বসে থাকলে চলবে না। জীবজগৎ যন্ত্র নয়; কাজেই যন্ত্র হিসেবে চিন্তা করা বাদ দিতে পারলে এর পেছনে আর কোনো ডিজাইন বা পরিকল্পনার মতো ‘উদ্দেশ্য খোঁজার দরকার নেই। জীবজগতে চোখ বা এধরনের জটিল। প্রত্যঙ্গের উদ্ভব ও বিবর্তনের পেছনে ডারউইন প্রস্তাব করলেন এক ‘অন্ধ কারিগরের’, নাম প্রাকৃতিক নির্বাচন যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লাখ লাখ বছর ধরে ধাপে ধাপে গড়ে ওঠা পরিবর্তনের ফলে চোখের মতো অত্যন্ত জটিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গড়ে ওঠা সম্ভব। এ প্রক্রিয়াটির নাম ক্রমবর্ধমান নির্বাচন (Cumulative selection। একাধিক ধাপের এই ক্রমবর্ধমান নির্বাচনের মাধ্যমে ধাপে ধাপে যে জটিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উদ্ভূত হতে পারে তা ইতোমধ্যেই বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।
ছবি। পেজ ৪৫৯
চিত্র : ডারউইন দেখিয়েছেন যে, প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে ঘটা বিবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লাখ লাখ বছর ধরে ধাপে ধাপে গড়ে। ওঠা পরিবর্তনের ফলে কাঠঠোকরার ঠোঁটের মতো অত্যন্ত জটিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গড়ে ওঠা সম্ভব।
শুধু তাই নয়, এ পদ্ধতিতে আংশিকভাবে চোখের উৎপত্তি ও বিকাশ যে সম্ভব এবং তা বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশে যে একটি জীবের টিকে থাকার সম্ভাবনাকে অনেকাংশে বাড়িয়ে তুলতে পারে তারও অজস্র উদাহরণ রয়েছে আমাদের চারপাশে। বিবর্তন তত্ত্ব ডিজাইন আর্গুমেন্টকে। বাতিল করে দেয় বলেই আমরা আজ প্রজাতির ‘উৎপত্তির কথা বলি, ‘সৃষ্টি’র নয়। বিবর্তন তত্বই প্রথমবারের মতো আমাদের দেখিয়ে দিল যে, মানুষসহ অন্যান্য জীবের উদ্ভবের পেছনে কোনো স্বর্গীয় কারণ খোঁজার দরকার নেই; অন্যান্য পশুপাখি, গাছপালা প্রাকৃতিক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে এ পৃথিবীতে এসেছে, মানুষ নামের দ্বিপদী প্রাণীটিও ঠিক একই বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় এ পৃথিবীতে এসেছে, কোনো ধরনের ‘সৃষ্টি’ (কিংবা সৃষ্টিকর্তার হস্তক্ষেপ) ছাড়াই। বিবর্তন তত্ব কীভাবে সৃষ্টির পরিকল্প যুক্তি বা ডিজাইন আর্গুমেন্টকে সরাসরি বাতিল করে দেয়, সেটার তেরো পর্বের একটা flaps (written by Dylan Evans & Howard Selina) রাখা আছে মুক্তমনা সাইটে[৩৫০]। এর দার্শনিক অভিব্যক্তি এতই বিশাল ছিল যে, অধ্যাপক ডকিন্স বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, ডেভিড হিউম কিংবা বার্ট্রান্ড রাসেলেরা ঈশ্বরের অস্তিত্বের যুক্তিগুলো বহুভাবে খণ্ডন করলেও ডারউইনের বিবর্তন তত্বই তাকে intellectually fulfilled atheist’-এ রূপান্তরিত করতে পেরেছে অত্যন্ত সার্থকতার সাথে। দার্শনিক ড্যানিয়েল ডেনেট সেজন্যই তার একটি বইয়ে বিবর্তন তত্বকে রাজাম্ল বা ইউনিভার্সাল এসিড’ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।
যা হোক, লেখার এই পর্যায়ে এসে অক্কামের ক্ষুরের ইতিহাসটি পাঠকদের সামনে একটু ছোট করে বান করতে চাচ্ছি। অক্কামের ক্ষুর’ নামক এই অদ্ভুতুড়ে পরিভাষাটি আসলে এসেছে ইংরেজ দার্শনিক উইলিয়াম অকহামের (William Ockham, ১২৪৫-১৩৪৯) নাম থেকে। অকহাম নিজে যদিও এই সূত্রটির উদ্ভাবক ছিলেন না, তবে এই সূত্রটি তিনি প্রায়শই বিভিন্নভাবে ব্যবহার করতেন বলে শোনা যায়। আর সেজন্যই তার নাম এই সূত্রের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। আমরা অবশ্য জানি না যে, নাপিতের ‘দাঁড়ি কামানোর ক্ষুরের মতো ভয়ংকর একটা কিছুর আদলে তার নাম নিয়ে এই উদ্ভট পরিভাষা সৃষ্টির সাথে তিনি একমত হতেন কিনা, তবে তিনি চান বা না চান তার নামটি কিন্তু বিখ্যাত এই সূত্রের সাথে আজ ওতপ্রোতভাবেই জড়িয়ে রয়েছে। ‘অক্কামের ক্ষুর’ মধ্যযুগীয় দর্শনের এক গুরুত্বপূর্ণ নীতি হিসেবে বিবেচিত হয়।
রসিকজনেরা কিন্তু এই সূত্রটি নিয়ে নানা ধরনের রসিকতা করতেও ছাড়েন নি। যেমন কেউ কেউ এই সূত্রটিকে অভিহিত করেন ‘Kiss’ সূত্র (Keep it simple, stupid) হিসেবে। কেউবা এই সূত্রটির নির্যাসকে তুলে ধরেন এভাবে–
যখন কোথাও ঘোড়ার ডাক শোনো, তখন ঘোড়ার কথাই মাথায় রেখো, জেব্রা বা জিরাফের নয়।
বিখ্যাত চিত্রকর ও বিজ্ঞানী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯) ছিলেন অকহামের সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব। তিনিও তার মতো করে একটি ‘অক্কামের সূর’ তৈরি করেছিলেন। তার রচিত ‘অষ্কামের ক্ষুরটি ছিল এ রকম–
Simplicity is the ultimate sophistication
ইতিহাসে অক্কামের ফুরের একটি সার্থক প্রযোগের উল্লেখ পাওয়া যায় বিজ্ঞানী লাপ্লাস এবং নেপোলিয়নের একটি মজার ঘটনায়। মুক্তমনার প্রথম বই ‘আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী,[৩৫১] শেষ হয়েছিল এ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির উল্লেখে। তবে, ঘটনাটি বানানো কিছু নয়। ঘটনাটি আমাদের নজর কাড়ে বিখ্যাত জ্যোতির্পদার্থবিদ মেঘনাদ সাহার ‘হিন্দু ধর্ম-বেদ-বিজ্ঞান সম্পর্কিত একটি চিত্তাকর্ষক বাদানুবাদ থেকে (আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্মঃ অনিলবরণ রাযের সমালোচনার উত্তর, মেঘনাদ সাহা, মেঘনাদ রচনা সংকলন, শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলিকাতা, ১৯০৮, পৃষ্ঠা ১২৭-১৬৯ দ্র.)। বর্ণিত ঘটনাটি এরকম–
বিখ্যাত গণিতজ্ঞ লাপ্লাস তার সুবিখ্যাত ‘Mechanique Celeste’ গ্রন্থে গ্রহসমূহের এবং চন্দ্রের গতির খুব সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, গতিবিদ্যা ও মাধ্যাকর্ষণ দিয়ে পর্যবেক্ষিত সকল গ্রহগতির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা দান সম্ভব। তিনি যখন গ্রন্থটি নেপোলিয়নকে উৎসর্গ করার জন্য অনুমতি চাইতে গেলেন, তখন নেপোলিয়ন রহস্য করে বলেন,
মসিঁয়ে লাপ্লাস, আপনি আপনার বইয়ে বেশ ভালোভাবেই মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের চালচলন ব্যাখ্যা করেছেন; কিন্তু আমি দেখলাম আপনি কোথাও ঈশ্বরের নাম উল্লেখ করেন নি। আপনার মডেলে ঈশ্বরের স্থান কোথায়?
লাগ্লাস উত্তরে বললেন, স্যার, এই বাড়তি অনুকল্পের কোনো প্রয়োজন নেই।
.
ঈশ্বরই কি সৃষ্টির আদি বা প্রথম কারণ?
বার্ট্রান্ড রাসেল তার বিখ্যাত ‘Why I am not a Christian প্রবন্ধে প্রথম কারণ সম্বন্ধে বলেন–
আমাদের আগেই বুঝে রাখা দরকার যে জগতের যা কিছু আমরা দেখতে পাই, সবকিছুর একটি কারণ আছে। এই কারণকে প্রশ্ন করতে করতে আপনি পেছনের দিকে এগিয়ে গিয়ে অবশ্যই প্রথম কারণের (First Cause) সম্মুখীন হবেন, এবং এই প্রথম কারণকেই স্বতঃসিদ্ধভাবে ‘ঈশ্বর হিসেবে ধরে নেওয়া হয়।… আমিও বহুদিন ধরেই এটিকে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছিলাম কিন্তু একদিন, যখন আমার বয়স আঠারো, আমি জন স্টুয়ার্ট মিলের আত্মজীবনী পড়ছিলাম, আর পড়তে গিযেই সেখানে এই বাক্যটি পেলাম: ‘আমার বাবা আমাকে প্রশ্ন করলেন। ‘কে আমাকে তৈরি করেছে?” আমি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি নি। কিন্তু এই প্রশ্নটি আমাকে আরও একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্নের দিকে ঠেলে দিল। যেটি হলো ঈশ্বরই যদি আমাকে তৈরি করে থাকেন, তবে ঈশ্বরকে তৈরি করেছে কে? আমি এখনও মনে করি ঈশ্বরকে তৈরি করেছে কে? এই সহজ সরল বাক্যটি প্রথম কারণ সম্পর্কিত যুক্তির দোষটি। সেই প্রথম আমাকে দেখালো। যদি প্রতিটি জিনিসের একটি কারণ থাকে, তবে ঈশ্বরেরও কারণ থাকতে হবে। আবার যদি কারণ ছাড়াই কোনোকিছু থাকতে পারে (যেমন ঈশ্বর), তবে এই যুক্তি ঈশ্বরের জগতের জন্যও সমানভাবে প্রযোজ্য।
‘বিগব্যাং তত্বটি বৈজ্ঞানিক সমাজে গৃহীত হওয়ার পর পরই বিশ্বাসীদের মধ্যে নতুন করে প্রথম কারণটিকে প্রতিষ্ঠিত করার নব উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেল। ১৯৫১ সালে Pope Pius XII পন্টিফিকাল অ্যাকাডেমির সভায় বলেই বসলেন–
যদি সৃষ্টির শুরু থাকে, তবে অবশ্যই এই সৃষ্টির একজন স্রষ্টাও রয়েছে, আর সেই স্রষ্টাই হলেন ঈশ্বর।
জ্যোর্তিবিজ্ঞানী এবং ধর্মযাজক জর্জ হেনরি লেমিত্রি (যিনি ‘বিগব্যাং’ প্রতিভাসের একজন অন্যতম প্রবক্তা) পোপকে সেসময় বিনয়ের সঙ্গে এধরনের যুক্তিকে ‘অভ্রান্ত’ হিসেবে প্রচার করা থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।
ইদানীংকালে ‘কালাম কসমোলজিক্যাল আর্গুমেন্ট (Kalam Cosmological Argument) নামে একটি দার্শনিক যুক্তিমালা সাধারণ বিশ্বাসীদের কাছে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত সুদর্শন দার্শনিক এবং পেশাদার বিতার্কিক উইলিয়াম লেন ক্রেইগ (William Lane Craig) ১৯৭৯ সালে লেখা The Kalam Cosmological Argument বইয়ের মাধ্যমে যুক্তির এই ধারাকে সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় করে তোলেন। ধারাটিকে নিচের চারটি ধাপের সাহায্যে বর্ণনা করা যায়–
১। যার শুরু (উৎপত্তি) আছে, তার পেছনে একটি কারণ রয়েছে।
২। আমাদের আজকের এই মহাবিশ্বের একটি উৎপত্তি আছে।
৩। সুতরাং এই মহাবিশ্বের পেছনে একটি কারণ আছে।
৪। সেই কারণটিই হলো ‘ঈশ্বর।
দার্শনিকেরা কালামের যুক্তিকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছেন বিভিন্ন সময়েই[৩৫২]। এ বইয়েও কয়েকটি প্রবন্ধে ‘আদি কারণের’ যুক্তিগুলোর খণ্ডন অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখানে ‘বাহুল্য বিধায় সেগুলোর পুনরুল্লেখ করা হলো
। তবে একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার উল্লেখ না করলেই নয়। সবকিছুর পেছনেই কারণ আছে বলে পেছাতে পেছাতে বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের কাছে গিয়ে হঠাৎ করেই থেমে যান। এ সময় আর তারা যেন কোনো কারণ খুঁজে পান না। মহাবিশ্বের জটিলতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য যদি ঈশ্বর নামক একটি সার আমদানি করতেই হয়, তবে সেই ঈশ্বরকে ব্যাখ্যা করার জন্য একই যুক্তিতে আরেকটি ‘ঈশ্বর’কে কারণ হিসেবে আমদানি করা উচিত। তারপর সেই ঈশ্বরের ঈশ্বর’-এর অস্তিত্ব ব্যাখ্যার জন্য লাগবে আরেকজন ঈশ্বর। এভাবে আমদানির খেলা চলতেই থাকবে একের পর এক, যা আমাদেরকে অসীমের দিকে ঠেলে দেবে। এই ব্যাপারটি স্বাভাবিকভাবেই সকল বিশ্বাসীদের কাছে আপত্তিকর। তাই ধর্মবাদীরা নিজেরাই ‘সবকিছুর পেছনেই কারণ আছে এই স্বতঃসিদ্ধের ব্যতিক্রম হিসেবে ঈশ্বরকে কল্পনা করে থাকেন আর সোচ্চারে ঘোষণা করেন ঈশ্বরের অস্তিত্বের পেছনে কোনো কারণের প্রয়োজন নেই। সমস্যা হলো যে, এই ব্যতিক্রমটি কেন শুধু ঈশ্বরের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে, মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে কেন নয় এর কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা তারা দিতে পারেন না।
দর্শন ছেড়ে এবার বিজ্ঞানের দিকে চোখ ফেরানো যাক। ‘যার শুরু আছে তার পেছনে কারণ থাকতেই হবে’-কালামের যুক্তিমালার প্রাথমিক ধাপটিকে বিজ্ঞানের জগতে অনেক আগেই খণ্ডন করা হয়েছে কারণবিহীন কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের উদাহরণ হাজির করে।
আণবিক পরিবৃত্তি, আণবিক নিউক্লিয়াসের তেজস্ক্রিয় অবক্ষয়ের মতো কোয়ান্টাম ঘটনাসমূহ ‘কারণবিহীন ঘটনা হিসেবে ইতোমধ্যেই বৈজ্ঞানিক সমাজে স্বীকৃত। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা তত্ত্ব অনুযায়ী সামান্য সময়ের জন্য শক্তি উৎপন্ন ও বিনাশ ঘটতে পারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোনো কারণ ছাড়াই। এগুলো সবগুলোই পরীক্ষিত সত্য। কাজেই উপরের উদাহরণগুলোই কালামের যুক্তিকে খণ্ডন করার জন্য যথেষ্ট।
সম্প্রতি বিজ্ঞানী লরেন্স ক্রাউস তার লেখা A Universe from Nothing[৩৫৩] বইটিতে তথাকথিত শূন্য থেকে কীভাবে জড় কণিকা উদ্ভূত হয় তা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। বহু বিজ্ঞানীই আজ মনে করেন এক কারণবিহীন কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের (Quantum Fluctuation) মধ্য দিয়ে এই মহাবিশ্বের উৎপত্তি হতে পারে, যা পরবর্তীকালে সৃষ্ট মহাবিশ্বকে স্ফীতির (Inflation) দিকে ঠেলে দিয়েছে, এবং আরও পরে পদার্থ আর কাঠামো তৈরির পথ সুগম করেছে[৩৫৪]। এগুলো কোনো কল্পকাহিনি নয়। মহাবিশ্ব যে শূন্য থেকে উৎপন্ন হতে পারে প্রথম এ ধারণাটি ব্যক্ত করেছিলেন এডওয়ার্ড ট্রিয়ন ১৯৭৩ সালে ‘নেচার’ নামক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জার্নালে[৩৫৫]। এরপর আশির দশকে স্ফীতি তত্ত্বের আবির্ভাবের পর থেকেই বহু বিজ্ঞানী প্রাথমিক কোয়ান্টাম ফ্লাকচুযেশনের ধারণাকে স্ফীতি তত্বের সাথে জুড়ে দিয়ে মডেল বা প্রতিরূপ নির্মাণ করেছেন। শুন্য থেকে এই মহাবিশ্ব উৎপত্তির ধারণা যদি অবৈজ্ঞানিক এবং ভ্রান্তই হতো, তবে সেগুলো প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক সাময়িকী (Scientific Journal) গুলোতে কখনোই প্রকাশিত হতো না। মূলত স্ফীতি তত্বকে সাম্প্রতিককালে বেশ কিছু পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়েছে, এবং প্রায় সবগুলোতেই এই তত্ব অত্যন্ত সাফল্যের সাথে এ পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয়েছে[৩৫৬]। স্ফীতি তত্ব গ্যালাক্সির ক্লাস্টারিং, এক্স রশ্মি এবং অবলোহিত তেজস্ক্রিয়তার বিন্যাস, মহাবিশ্বের প্রসারণের হার এবং এর ব্যস, মহাবিশ্ব গঠনে এর উপাদানগুলোর প্রাচুর্য সবকিছুই ব্যাখ্যা করতে পেরেছে নিখুঁত সৌন্দর্যে। এর কারিগরি দিকগুলো এখানে আলোচনা করছি না, এগুলো নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে অভিজিৎ রায় এবং মীজান রহমানের ‘শূন্য থেকে মহাবিশ্ব বইয়ে[৩৫৭]।
আসলে ইনফ্লেশন বা স্ফীতি নিয়ে আঁদ্রে লিন্ডে আর তার দলবলের সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফল যদি সত্যি হয়ে থাকে তবে সত্যিকার অর্থেই সেই উত্তপ্ত বিগব্যাং যার মাধ্যমে পনেরো শ’ কোটি বছর আগে এক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে এ মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে বলে ধারণা করা হয়, তাকে বিদায় জানানোর সময় এসে গিয়েছে। কারণ, সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, বিগব্যাং দিয়ে মহাবিশ্বের শুরু নয়, বরং মহাবিশ্বের শুরু হয়েছে ইনফ্লেশন দিয়ে। অর্থাৎ, বিগব্যাং-এর পরে ইনফ্লেশনের মাধ্যমে মহাবিশ্ব তৈরি (যা কিছুদিন আগেও সত্যি বলে ভাবা হতো) হয় নি, বরং ইনফ্লেশনের ফলশ্রুতিতেই কিন্তু বিগব্যাং হয়েছে, তারপর সৃষ্ট হয়েছে আমাদের মহাবিশ্ব। তার কথায়[৩৫৮]–
Inflation is not a part of big-bang theory as we thought 15 years ago. On the contrary, the big-bang is the part of inflationary model.
আরও মজার ব্যাপার হলো, ওই ইনফ্লেশনের ফলে শুধু যে একবারই বিগব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ ঘটেছে তা কিন্তু নয়, এরকম বিগব্যাং কিন্তু হাজার হাজার কোটি কোটি এমনকি অসীমসংখ্যকবার ঘটতে পারে; তৈরি হতে পারে অসংখ্য ‘পকেট মহাবিশ্ব। আমরা সম্ভবত এমনই একটি পকেট-মহাবিশ্বে অবস্থান করছি বাকিগুলোর অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞাত না হয়ে (এ ব্যাপারটিকে বলা হয় ‘মাল্টিভার্স বা অনন্ত মহাবিশ্বের ধারণা[৩৫৯])। এই ধারণা অনুযায়ী আমাদের মহাবিশ্ব যাকে এতদিন প্রকৃতির পুরো অংশ বলে ভেবে নেওয়া হতো, আসলে হয়ত এটি এক বিশাল কোনো অমনিভার্স (Omniverse)-এর খুব ক্ষুদ্র অংশবিশেষ ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের অবস্থাটা এতদিন ছিল সেই বহুল প্রচলিত ‘অন্ধের হস্তি দর্শন গল্পের অন্ধ লোকটির মতো হাতির কান ছুঁযেই যে ভেবে নিয়েছিল ওইটাই বুঝি হাতির পুরো দেহটা! যাহোক, নিচের ছবিটি দেখলে লিন্ডের সাম্প্রতিক স্ফীতি তত্বটি (যেটির নামকরণ করা হয়েছে Chaotic inflation) কী বলতে চাইছে এ সম্বন্ধে হয়ত কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে।
ছবি। পেজ ৪৬৯
SELF-REPRODUCING COSMOS appears as an extended branching of bubbles. Changes in color represent ‘mutations” in the laws of plıysic ent universes. The properties of space in each bubble do not depend when the bubble formed. In this sense, the universe as a whole may be even though the interior of each bubble is described by the big bang ti
চিত্র : লিন্ডের সাম্প্রতিক তত্ব বলছে কেওটিক ইনফ্লেশনের ফলে উৎপত্তি হয়েছে অসংখ্য সম্প্রসারিত বুদ্বুদ এবং প্রতিটি সম্প্রসারিত বদ্বুদই আবার জন্ম দিয়েছে এক একটি ‘বিগব্যাং-এর। আর সেই এক একটি বিগব্যাং পরিশেষে জন্ম দিয়েছে এক একটি পকেট মহাবিশ্বের। আমরা এধরনেরই একটি পকেট মহাবিশ্বে বাস করছি (ছবির উৎস-সায়েন্টিফিক আমেরিকান)।
দেখা যাচ্ছে, এ তত্ত্ব অনুযায়ী কেওটিক ইনফ্লেশনের ফলে উৎপত্তি হয়েছে অসংখ্য সম্প্রসারিত বুদ্বুদ (Expanding Bubbles) এবং প্রতিটি সম্প্রসারিত বদ্বুদই আবার জন্ম দিয়েছে এক একটি ‘বিগব্যাং-এর। আর সেই এক একটি বিগব্যাং পরিশেষে জন্ম দিয়েছে এক একটি পকেট মহাবিশ্বের। আমরা এধরনেরই একটি পকেট মহাবিশ্বে বাস করছি। এ তত্ব আজ অনেকের মাঝেই তৈরি করেছে ‘সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কাঁপা’ এক সর্বজনীন দার্শনিক আবেদনের এ মহাবিশ্ব যদি কোনো দিন ধ্বংস হয়ে যায়ও, জীবনের মূল সত্ত্বা হয়ত টিকে থাকবে অন্য কোনো মহাবিশ্বে, হয়ত অন্য কোনোভাবে, অন্য কোনো পরিসরে
লিন্ডের মতে এ তত্বের সমাধানটি এতটাই সরল যে, এর আগে এটি বিজ্ঞানীদের মাথায় কেন আসে নি তা ভেবে লিন্ডে নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছেন। অ্যালেন গুথ, যাকে ইনফ্লেশন তত্ত্বের জনক হিসেবে অভিহিত করা। হয়, তিনি তার ‘দ্য ইনফ্লেশনারি ইউনিভার্স বইয়ে মহাবিশ্বের উদ্ভবকে একটি ‘আল্টিমেট ফ্রি লাঞ্চ হিসেবে অভিহিত করে বলেন–
Most important of all, the Question of the Origin of the matter in the Universe is no longer thought to be beyond of science. … If inflation is correct, then the inflationary mechanism is responsible for creation of essentially all the matter and energy in the Universe. … After two thousand years of scientific research, it now seems likely that Lucretius (who said ‘Nothing can be created from nothing’) was wrong. Conceivably, everything can be created from nothing. And ‘everything’ might include a lot more than what we can see. In the context of inflationary cosmology, it is fair to say that Universe is the ultimate free lunch!
অনেক বিজ্ঞানী এবং দার্শনিকেরাই মনে করেন, কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের ধারণার সাথে সমন্বিত করা ইনফ্লেশন বা স্ফীতি তত্ব যখন একেবারে শূন্য থেকে মহাবিশ্বের উৎপত্তির একটি প্রাকৃতিক এবং যৌক্তিক সমাধান দিতে পারছে, তখন ঈশ্বর সম্ভবত একটি বাড়তি হাইপোথিসিস’ ছাড়া আর কিছু নয়।
ইনফ্লেশন বা স্ফীতি তত্ব ছাড়াও আরেকটি তত্ব মহাবিশ্বকে ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে ইদানীং জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পল স্টাইনহার্ট এবং নেইল টুরকের প্রস্তাবিত এই চক্রাকার মহাবিশ্ব বা ‘সাইক্লিক মডেলে’ তারা দেখিয়েছেন আমাদের মহাবিশ্বের কোনো শুরু নেই, শেষ নেই। এ এক চলমান অনন্ত, অফুরন্ত মহাবিশ্ব (endless universe)। তাদের আঁকা এ ছবিতে ‘বিগব্যাং দিয়ে স্থান কালের (space-time) শুরু নয়, বিগব্যাং–কে তারা দেখিয়েছেন কেবল একটি ঘটনা হিসেবে যার উদ্ভব হয় স্ট্রিং তাত্বিকদের কথিত দুটো ব্রেনের সংঘর্ষের (collision of branes) ফলে। এবং কেবল একবারই এই মহাবিস্ফোরণ ঘটবে বা ঘটেছে তাও নয়, বরং এ মহাবিশ্ব প্রাকৃতিক বিবর্তনের চক্রে চির চলমান। তারা গাণিতিকভাবে দেখিয়েছেন, মহাবিশ্বের যাত্রাপথের প্রতিটি চক্রে বিগব্যাং উদ্ভব ঘটায় উত্তপ্ত পদার্থ এবং শক্তির। কালের পরিক্রমায় ক্রমশ শীতল হয়ে এর থেকে তৈরি হয় গ্যালাক্সি আর তারকারাজি, যা আমরা আজ চোখ মেললেই দেখতে পাই। আজ থেকে ট্রিলিয়ন বছর পরে আবারও বিগব্যাং ঘটবে এবং তৈরি করবে নতুন চক্রের। পল স্টেইনহার্ট এবং নেইল টুরক তাদের প্রস্তাবিত মডেলকে সাধারণ পাঠকদের কাছে নিয়ে এসেছেন সম্প্রতি ‘Endless Universe’ বইয়ের মাধ্যমে[৩৬০]। নতুন এ তত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্বের যেহেতু কোনো শুরু’ নেই, এর পেছনে কোনো স্রষ্টা বসানোর চেষ্টা অর্থহীন। বিশ্বাসীদের অতি-প্রিয় কালামের যুক্তিমালা এ মডেলের জন্য একেবারেই প্রায়োগিক নয়।
ছবি। পেজ ৪৭২
চিত্র : পল স্টেইনহার্ট এবং নেইল টুরক তাদের প্রস্তাবিত এই চক্রাকার মহাবিশ্ব বা ‘সাইক্লিক মডেলে’ দেখিয়েছেন আমাদের মহাবিশ্বের কোনো শুরু নেই, শেষ নেই, এবং পদার্থ এবং শক্তির উদ্ভব হয় দুটো ব্রেনের সংঘর্ষের ফলশ্রুতিতে, এবং এই প্রক্রিয়া চলতে থাকবে অনন্তকাল।
মহাবিশ্বের সত্যিকার প্রকৃতি বোঝার জন্য হয়ত আমাদের ভবিষ্যতের কারিগরি জ্ঞানের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে, তবে এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইনফ্লেশনারি কিংবা সাইক্লিক যে মহাবিশ্বই ভবিষ্যতে সঠিক প্রমাণিত হোক না কেন, এ দুটি তত্বের কোনো তই তাদের তত্ত্বকে সার্থকতা দেওয়ার জন্য কোনো অলৌকিক সত্বর উপর নির্ভর করছে না, মডেলগুলো নির্মাণ করা হয়েছে আমাদের জানা শোনা পদার্থবিজ্ঞানের নিয়ম নীতি অনুসরণ করেই।
আরেকটি কথা বলা প্রাসঙ্গিক হবে এ ব্যাপারে। বিজ্ঞান কিন্তু কোনো বিষয় সম্পর্কে পরম বা নিখুঁত জ্ঞান দিতে পারে না। আজকে আণবিক স্থানান্তর, নিউক্লিয়াসের তেজস্ক্রিয় বিকিরণ বা কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশনের মতো ঘটনার কারণ পাওয়া যাচ্ছে না, ভবিষ্যতে পাওয়া যেতেই পারে। কেউই সে সম্ভাবনাকে অস্বীকার করছে না। ভবিষ্যতে পাওয়া যেতে পারে মহাবিশ্বের অস্তিত্বের পেছনের ‘আদি’ কারণও। কিন্তু সেই কারণটি যে ঈশ্বরের মতো মহাপরাক্রমশালী ‘সত্ত্বা’ই হতে হবে, এটি ভেবে নেওয়ার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই, বরং কারণটি হতে পারে সম্পূর্ণভাবেই ‘প্রাকৃতিক। ওযেস মরিসন তার ‘Must the Beginning of the Universe Have a Personal Cause? A Critical Examination of the Kalam’s Cosmological Argument’-এ বলেন–
সৃষ্টির সবকিছুর পেছনেই কারণ আছে এ ব্যাপারটি ধ্রুব সত্য নয়। আর যদিও বা ইতিহাসের পরিক্রমায় কখনও বের হয়ে আসে যে মহাবিশ্ব সৃষ্টির পেছনে একটি ‘আদি’ কারণ রয়েছেই, তবুও একথা ভেবে নেওয়ার কারণ নেই। যে, সেই আদি কারণটি ঈশ্বরের মতো একটি ব্যক্তি সম্বাই হতে হবে।
পদার্থবিদ ড. ভিক্টর স্টেঙ্গরও একই ধরনের মত ব্যক্ত করে বলেন–
ধরে নিলাম কালামের কথা অনুযায়ী মহাবিশ্বের একটি কারণ রয়েছেই, তো সেই একটা কারণ কেন স্রেফ প্রাকৃতিক কারণ হতে পারবে না? কাজেই দেখা যাচ্ছে কালামের যুক্তিমালা প্রায়োগিক এবং তাত্বিক দুদিক থেকেই ব্যর্থ হচ্ছে।
.
নাস্তিকতাও একটি ধর্ম (বিশ্বাস) হলে…
আমরা দেখেছি অনেকেই বুঝে হোক, না বুঝে হোক, এই ব্যাপারটি মাঝে মধ্যে এভাবেই আউড়ে দেন যে, আস্তিক্যবাদের মতো নাস্তিক্যবাদও এক ধরনের বিশ্বাস। আস্তিকরা যেমন ঈশ্বর আছে এই মতবাদে বিশ্বাস করে, তেমন নাস্তিকরা বিশ্বাস করে ঈশ্বর নেই’-এই মতবাদে। দুটোই নাকি বিশ্বাস। যেমন, একবার মুক্তমনা ব্লগে এক ভদ্রলোক তর্ক করতে গিয়ে বলে বসলেন–
নাস্তিক মানেই বিশ্বাসী। তারা বিশ্বাস করে যে ঈশ্বর নেই। কিন্তু ঈশ্বর নেই’ এটি প্রমাণিত সত্য নয়। শুধু যুক্তি দিয়েই বোঝানো সম্ভব ঈশ্বর নেই’ বিবৃতিটি আসলে ফাঁকিবাজি।
নাস্তিক মানেই বিশ্বাসী, কিংবা নাস্তিকতাবাদও একটি বিশ্বাস এগুলো ঢালাওভাবে আউড়ে দিয়ে নাস্তিকতাবাদকেও এক ধরনের ‘ধর্ম হিসেবে হাজির করার চেষ্টাটি আমরা বহু মহলেই দেখেছি। নাস্তিকদের এভাবে সংজ্ঞায়ন সঠিক কি ভুল, তা বুঝবার আগে ‘নাস্তিক’ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থটি আমাদের জানা প্রয়োজন। নাস্তিক’ শব্দটি ভাঙলে দাঁড়ায়, নাস্তি + কন বা নাস্তিক। নাস্তি’ শব্দের অর্থ হলো নাই, অবিদ্যমান। ‘নাস্তি’ শব্দটি মূল সংস্কৃত হতে বাংলায় এসে ‘ক’ বা ‘কন’ প্রত্যয় যোগে নাস্তিক হয়েছে যা তৎসম শব্দ হিসেবে গৃহীত। ন আস্তিক = নাস্তিক যা নঞ তৎপুরুষ সমাসে সিদ্ধ এবং আস্তিকের বিপরীত শব্দ। আরও সহজ বাংলায় বললে বলা যায়, না + আস্তিক = নাস্তিক। খুবই পরিষ্কার যে, সঙ্গত কারণেই আস্তিকের আগে ‘না’ প্রত্যয় যোগ করে নাস্তিক শব্দটি তৈরি করা হয়েছে। আস্তিকরা যে ঈশ্বর/আল্লাহ/খোদা ইত্যাদি পরম সত্ত্বায় বিশ্বাস করে এ তো সবারই জানা। কাজেই নাস্তিক হচ্ছে তারাই, যারা এই ধরনের বিশ্বাস হতে মুক্ত। তাই সংজ্ঞানু্যায়ী নাস্তিকতা কোনো বিশ্বাস নয়, বরং বিশ্বাস হতে মুক্তি বা বিশ্বাসহীনতা। ইংরেজিতে নাস্তিকতার প্রতিশব্দ হচ্ছে। ‘Atheist?l সেখানেও আমরা দেখছি theist শব্দটির আগে ‘a প্রিফিক্সটি জুড়ে দিয়ে Atheist শব্দটি তৈরি করা হয়েছে। নাস্তিকতা এবং মুক্তচিন্তার উপর বহুল প্রচারিত গবেষণাধর্মী একটি ওযেবসাইটে শব্দটির সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে এভাবে–
Atheism is characterized by an absence of belief in the existence of gods. This absence of belief generally comes about either through deliberate choice, or from an inherent inability to believe religious teachings which seem literally incredible. It is not a lack of belief born out of simple ignorance of religious teachings.
সহজেই অনুমেয় যে, ‘absence of belief’ শব্দমালা চয়ন করা হয়েছে ‘বিশ্বাসহীনতা’কে তুলে ধরতেই, উল্টোটি বোঝাতে নয়। Gordon Stein তার বিখ্যাত ‘An Anthology of Atheism and Rationalism’ বইয়ে নাস্তিকতার (Atheism) সংজ্ঞায়ন করতে গিয়ে বলেন–
When we examine the components of the word ‘atheism,’ we can see this distinction more clearly. The word is made up of ‘a-’ and—theism.’ Theism, we will all agree, is a belief in a God or gods. The prefix ‘a-’ can mean ‘not’ (or ‘no’) or ‘without. If it means ‘not,’ then we have as an atheist someone who is not a theist (i.e., someone who does not have a belief in a God or gods). If it means ‘without,’ then an atheist is someone without theism, or without a belief in God. (Atheism and Rationalism, p. 3. Prometheus, 1980)
আমরা যদি atheist শব্দটির আরও গভীরে যাই তবে দেখব যে, এটি আসলে উদ্ভূত হয়েছে গ্রিক শব্দ ‘a’ এবং ‘theos’ হতে। গ্রিক ভাষায় ‘theos’ বলতে বোঝায় ঈশ্বরকে, আর ‘a’ বলতে বোঝায় অবিশ্বাস বা বিশ্বাসহীনতাকে। সেজন্যই Michael Martin তার ‘Atheism : A Philosophical Justification বইয়ে বলেন–
According to its Greek roots, then, atheism is a negative view, characterized by the absence of belief in God. (Atheism : A Philosophical Justification’, p. 463.,Temple University Press, 1990)
আসলে নাস্তিকদের বিশ্বাসী দলভুক্ত করার ব্যাপারটি খুবই অবিবেচনাপ্রসূত। ব্যাপারটাকে আরেকটু পরিষ্কার করা যাক। ধরা যাক, এক মুক্তমনা যুক্তিবাদী ব্যক্তি ভূতে বিশ্বাস করেন না। তবে কি সেজন্য তিনি ‘না-ভূতে বিশ্বাসী হয়ে গেলেন? উনাদের যুক্তি অনুযায়ী তাই হওয়ার কথা। এভাবে দেখলে, প্রতিটি অপ-বিশ্বাস বিরোধিতাই তাহলে উল্টোভাবে ‘বিশ্বাস বলে চালিয়ে দেওয়া যায়, তা সে ভূতই হোক, পঙ্খিরাজ ঘোড়াই হোক, অথবা ঘোড়ার ডিমই হোক। যিনি পঙ্খিরাজ ঘোড়া বা চাঁদের চরকা-বুড়ির অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, তিনি আসলে তার সংশয় এবং অবিশ্বাস থেকেই তা করেন না, তার ‘না-বিশ্বাসে বিশ্বাসী হওয়ার কারণে নয়। যদি ওই ব্যক্তিটিকে জিজ্ঞাসা করা হয়, কেন ওগুলোতে তিনি বিশ্বাস করেন না, তিনি হয়ত জবাবে বলবেন, ওগুলোতে বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নি বলে। কিংবা হয়ত বলতে পারেন, এখন পর্যন্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ওগুলো সত্ত্বার বাস্তব অস্তিত্ব কেউ প্রমাণ। করতে পারেন নি, তাই ওসবে বিশ্বাস করার প্রশ্ন ওঠে না। এটি পরিষ্কার যে, এই বক্তব্য থেকে তার মনের সংশয় আর অবিশ্বাসের ছবিটিই আমাদের সামনে মূর্ত হয়ে ওঠে, বিশ্বাসপ্রবণতাটি নয়। ঈশ্বরে অবিশ্বাসের ব্যাপারটিও কিন্তু তেমনই। নাস্তিকেরা তাদের সংশয় আর অবিশ্বাস থেকেই নাস্তিক হন, ‘না-ঈশ্বরে বিশ্বাস থেকে নয়। সে জন্যই মুক্তমনা Dan Barker তার বিখ্যাত ‘Losing Faith in Faith: From Preacher to Atheist’ গ্রন্থে পরিষ্কার করেই বলেছেন ‘Basic atheism is not a belief. It is the lack of belief.’ (পৃ. ৯৯)। আসলে সত্যি বলতে কী, ‘বিশ্বাস ব্যাপারটিই দাঁড়িয়ে আছে একটি ‘অপ-বিশ্বাসমূলক প্রক্রিয়ার উপর। ড. হুমায়ুন আজাদের একটি উক্তিও এখানে খুব প্রাসঙ্গিক। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন,
যে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই, যার কোনো অস্তিত্ব নেই যা প্রমাণ করা যায় না, তাতে মানুষকে বিশ্বাস করতে হয়। মানুষ ভূতে বিশ্বাস করে, পরীতে বিশ্বাস করে বা ভগবানে, ঈশ্বরে বা আল্লায় বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাস সত্য নয়, এগুলোর কোনো বাস্তবরূপ নেই। মানুষ বলে না, আমি গ্লাসে বিশ্বাস করি বা পানিতে বিশ্বাস করি, মেঘে বিশ্বাস করি। যেগুলো নেই সেগুলোই মানুষ বিশ্বাস করে। বিশ্বাস একটি অপবিশ্বাসমূলক ক্রিয়া। যা সত্য, তাতে বিশ্বাস করতে হয় না; যা মিথ্যে তাতে বিশ্বাস করতে হয়। তাই মানুষের সব বিশ্বাস ভুল বা ভ্রান্ত, তা অপবিশ্বাস।
নাস্তিকেরা সঙ্গত কারণেই এই সমস্ত প্রথাগত অপবিশ্বাসের বাইরে। ঈশ্বর নেই’ বিবৃতিটি যদি ‘পলিটিকালি কারেক্ট সংশ্যবাদীদের কাছে ‘ফাঁকিবাজি’ হয়, তবে অশ্বত্থামা, ট্যাঁশ গরু, বকচ্ছপ, থর জিউস, জলপরী, ফ্লাইং স্পেগেটি মনস্টার এগুলো নেই বলাও এক ধরনের ফাঁকিবাজি’।
ধর্মকারী নামে একটি সাইট আছে আন্তর্জালে। সাইটটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে-’যুক্তিমনস্কদের নির্মল বিনোদনের ব্লগ। এই ব্লগে ধর্মের যুক্তিযুক্ত সমালোচনা করা হবে, ধর্মকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হবে, অপদস্থ করা হবে, ব্যঙ্গ করা হবে। যেমন করা হয়ে থাকে সাহিত্য, চলচ্চিত্র, খেলাধুলা বা অন্যান্য যাবতীয় বিষয়কে। সেখানকার একটি পোস্ট থেকে কিছু অমৃতবচন উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না। নাস্তিক্যবাদকে ধর্মের সঙ্গে যারা তুলনা করে থাকে, তাদের বলতে ইচ্ছে করে–
১. নাস্তিক্যবাদ ধর্ম হলে ‘অফ বাটনকে টিভি চ্যানেল বলতে হয়।
২. নাস্তিক্যবাদ ধর্ম হলে টাককে বলতে হয়। চুলের রঙ।
৩. নাস্তিক্যবাদ ধর্ম হলে স্ট্যাম্প না জমানোকে হবি বলতে হ্যাঁ।
৪. নাস্তিক্যবাদ ধর্ম হলে বাগান না করাও একটি শখ, ক্রিকেট না খেলাও একটি ক্রীড়া, কোকেইন সেবন না করাও একটি নেশা।
এই চমৎকার উপমাগুলোর পাশাপাশি মুক্তমনা ব্লগে অনুরূপ কয়েকটি বাক্য উল্লেখ করে তালিকার শ্রীবৃদ্ধি করার চেষ্টা করেছিলাম, সেগুলো হয়ত পাঠকদের চিন্তার খোরাক যোগাবে–
‘নাস্তিকতা একটি বিশ্বাস হলে বোবা লোককে ‘ভাষাবিদ হিসেবে ডাকতে হয়।
নাস্তিকতা একটি বিশ্বাস হলে দন্তহীন ব্যক্তিকে ‘দাঁতাল’ আখ্যা দিতে হয়।
নাস্তিকতা একটি বিশ্বাস হলে উপোস থাকাকেও এক ধরনের ‘খাদ্যগ্রহণ’ বলতে হয়।
নাস্তিকতা একটি বিশ্বাস কিংবা ধর্ম হলে চাকরি না করাটাও একটি পেশা।
নাস্তিকতা একটি ধর্ম হলে বই না পড়াকেও বলতে হয় পাঠাভ্যাস।
নাস্তিকতা বিশ্বাস হলে পোশাক খুলে ফেলাটাও এক ধরনের পোশাক পরিধান।
নাস্তিকতা ধর্ম হলে চশমা না পরাটাও এক ধরনের সানগ্লাসের ফ্যাশন।
নাস্তিকতা একটি বিশ্বাস হলে চিরকৌমার্যও বিবেচিত হওয়া উচিত এক ধরনের ‘বিবাহ’ হিসেবে।
নাস্তিকতা একটি বিশ্বাস হলে নির্লোভ থাকার চেষ্টাকেও এক ধরনের ‘লোভ’ বলতে হয়।
নাস্তিকতা একটি ধর্ম হলে নিরোগ স্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়াটাও তাহলে এক ধরনের রোগ!
————
১ বইয়ের জগৎ, নবম সংকলন, মে ২০১২।
২ মুক্তমনা, এপ্রিল ৪, ২০১২ মুক্তমনা ইবুক
৩ মীজান রহমান এবং অভিজিৎ রায়,শূন্য থেকে মহাবিশ্ব,শুদ্ধস্বর,২০১৫ (প্রকাশিতব্য)
৪ অভিজিৎ রায়, বিশ্বাসের ভাইরাস, জাগৃতি, ২০১৪
৫ Stephen Hawking & Leonard Mlodinow, The Grand Design, Bantam; 1st Edition edition (September 7, 2010)
৬ Richard Dawkins, The God Delusion, Houghton Mifflin Harcourt, 2006
৭ Richard Dawkins, Viruses of the Mind, available online : http ://cscs.umich.edu/~crshalizi/Dawkins/viruses-of-the-mind.html
৮ Daniel C. Dennett, Breaking the Spell : Religion as a Natural Phenomenon, Penguin, 2007
৯ Darrel W. Ray, The God Virus : How religion infects our lives and culture, IPC Press, 2009
১০ Richard Brodie, Virus of the Mind : The New Science of the Meme, Hay
১১ House; Reprint edition, 2009 11 Richard Dawkins, The Selfish Gene, Oxford University Press, 1976
১২ Shaoni Bhattacharya, Parasites brainwash grasshoppers into death dive, New Scientists, August 2005
১৩ এই বইয়ের অষ্টম অধ্যায় দ্রষ্টব্য; এ ছাড়া পড়ুন, অভিজিৎ রায়, বিশ্বাসের ভাইরাস, জাগৃতি, ২০১৪।
Bruce Lincoln, Holy Terrors : Thinking about Religion after September 11, University Of Chicago Press; 1 edition, 2003
১৫ বাইবেলে তো আছেই (জেনেসিস ২:২১-২৫), সেই সাথে কোরআন শরিফের ৪:১, ৭:১৮৯, ৩০:২০-২১, ৩৯:৬ প্রভৃতি আয়াত দ্রষ্টব্য। আর হাদিসে আছে সরাসরি:
‘নারীদের প্রতি বন্ধুত্বমূলক আচরণ করো, কারণ তাদেরকে বুকের। হাড় থেকে তৈরি করা হয়েছে, বুকের বাঁকা হাড়, যদি তুমি তাকে সোজা করতে চাও তবে তা ভেঙে যাবে; আর যদি তুমি কিছুই না করো, তবে সে বাঁকাই থেকে যাবে।’ (বুখারি এবং মুসলিম)
১৬ Sam Harris, The End of Faith : Religion, Terror, and the Future of Reason, W. W. Norton, 2004
১৭. ব্লগার, ক্যাডেট কলেজ ব্লগ, http://www.cadetcollegeblog.com/arnob
১৮. অভিজিৎ রায়, আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৫ (পুনর্মুদ্রণ ২০০৬)
১৯. Stephen Hawking and, Leonard Mlodinow, The Grand Design, Bantam, 2010
২০. Victor J. Stenger, ‘The New Atheism’. Colorado University. http://www.colorado.edu/philosophy/vstenger/battle.html.
২১. Richard Dawkins, The God Delusion, Mariner Books; 1 edition, 2008
২২. ফরিদ আহমেদ, প্রার্থণা কি কোন কাজে আসে?, মুক্তমনা
২৩. Richard Dawkins, The God Delusion, Mariner Books; 1 edition, 2008 থেকে উদ্ধৃত।
২৪ Ted Honderich, The Oxford Companion to Philosophy, Oxford University Press, USA, 1995 25
২৫ অনুবাদটি মুক্তান্বেষা পত্রিকায় (১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা) কেন আমি সংশয়বাদী? শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে৷
২৬ অপার্থিব, স্বাধীন ইচ্ছা, মন্দ ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব, মুক্তমনা (স্বতন্ত্র ভাবনা : মুক্তচিন্তা ও বুদ্ধির মুক্তি, নির্বাচিত প্রবন্ধাবলী, সম্পাদক–সাদ কামালী ও অভিজিৎ রায়, অঙ্কুর প্রকাশনী)।
২৭ Victor J. Stenger, God : The Failed Hypothesis–How Science Shows That God Does Not Exist, Prometheus Books, 2008
২৮ Michael Martin Michael Martin and Ricki Monnier, The Impossibility of God, Prometheus Books, 2003
২৯ David Marshall, The Truth behind the New Atheism, Eugene, Or : Harvest House, 2007
৩০ উদাহরণ হিসেবে দেখতে পারেন, Richard Dawkins, Umweaving the Rainbow, Boston: Houghton Mifflin, 1998
৩১ অপার্থিব জামান, বিজ্ঞান, শিল্প ও নন্দনতত্ব, মুক্তান্বেষা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা।
৩২ David Berlinski, The Devil’s Delusion, New York : Crown Forum, 2008, পৃষ্ঠা নং ৬।
৩৩ David Berlinski, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা নং ৪
৩৪ Dinesh D’Souza, What’s So Great about Christianity?, Washington, DC : Regnery, 2007, পৃষ্ঠা নং ১৫৭
৩৫ Barry Palevitz, Science vs. Religion’ in Science and Religion : Are They Compatible? ed. Paul Kurtz, Amherst, NY : Prometheus Books, 2003, পৃষ্ঠা নং ১৭৫
৩৬ National Academy of Sciences, Teaching about Evolution and the Nature of Science (Washington, DC : National Academy of Science, 19 নং ৫৮। অনলাইন সংস্করণ : http ://www.nap.edu/catalog/5787.html
৩৭ Edward J. Larson, Leading scientists still reject God, Nature, Vol. 394, No. 6691, p. 313 (1998), Macmillan Publishers Ltd.
৩৮ Stephen Jay Gould, Rocks of Ages : Science and Religion in the Fullness of Life, Library of Contemporary Thought (New York : Ballantine, 1999
৩৯ (Richard Dawkins), ‘When Religion Steps on Science’s Turf The Alleged Separation Between the Two Is Not So Tidy’, Council for Secular Humanism. Brief paraphrase of: ‘There is something dishonestly self-serving in the tactic of claiming that all religious beliefs are outside the domain of science. On the one hand, miracle stories and the promise of life after death are used to impress simple people, win converts, and swell congregations. It is precisely their scientific power that gives these stories their popular appeal. But at the same time it is considered below the belt to subject the same stories to the ordinary rigors of scientific criticism : these are religious matters and therefore outside the domain of science. But you cannot have it both ways. At least, religious theorists and apologists should not be allowed to get away with having it both ways. Unfortunately all too many of us, including nonreligious people, are unaccountably ready to let them.’
৪০ অভিজিৎ রায়, নৈতিকতা ও ধর্ম, স্বতন্ত্র ভাবনা, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৮
৪১ H. Benson, J.A. Dusek, J.B. Sherwood, P.Lam, C.F. Bethea. ‘Study of the Therapeutic Effects of Intercessory Prayer (STEP) in Cardiac Bypass Patient, ‘American Heart Journal 151, no. 4:934-42
৪২ প্রার্থনা তো কোন কাজে আসেই না, হার্ভার্ড এবং মায়ো ক্লিনিকের তত্বাবধানে পরিচালিত স্টেপ স্টাডি থেকে প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে, কোন কোন ক্ষেত্রে প্রার্থনা বরং মানসিক উদ্বেগ বড়িয়ে তোলে। সে পরীক্ষায় যাদের জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে, দেখা গিয়েছিলো পরবর্তীতে তাদের অনেকেরই শারীরিক অবস্থার অবনমন ঘটেছে। এটা কেন হল গবেষকেরা হলফ করে বলতে পারেননি, তবে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হিসেবে তারা বলেছেন, যে সমস্ত রোগী জানতে পেরেছে যে তাদের জন্য প্রার্থনা করা হচ্ছে, তারা ভেবে নিয়েছে তাদের অবস্থা এতোটাই গুরুতর যে সঘবদ্ধ প্রার্থনার দরকার পড়ছে। ফলে তাদের মধ্যে উদ্বেগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে, আর সেই সাথে ঘটেছে শারীরিক জটিলতা বৃদ্ধি’। তবে ‘নেগেটিভ’ ফলাফলের ব্যাপারটা যদি আমরা বাদও দেই এটা নিশ্চিত, প্রার্থনার কোন সুপ্রভাব নেই, অন্তত নিরপেক্ষ গবেষণায় তা পাওয়া যায়নি।
৪৩ রায়হান আবীর, মানুষিকতা, শুদ্ধস্বর, ২০১৩
৪৪ Paul Davies, ‘Taking Science on Faith, ‘New York Times, November 24, 2007
৪৫ John F. Haught, God and the New Atheism, Westminster John Knox Press, 2007 পৃষ্ঠা নং ৪৬।
৪৬ অভিজিৎ রায়, নৈতিকতা ও ধর্ম, স্বতন্ত্র ভাবনা, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৮ দ্রষ্টব্য
৪৭ ইরতিশাদ আহমদ, বিজ্ঞানমনস্ক ধারা ধর্মাচ্ছন্ন স্রোতে, বিজ্ঞান ও ধর্ম : সংঘাত নাকি সমন্বয়? মুক্তমনা ই-বুক।
৪৮ Jhon William Draper, History of the Conflict between Religion and Science, London : Watts & Co., 1873
৪৯ Andrew Dickson White, A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom, New York : D. Appleton & CO.,1896
৫০ Paul Kurtz, ed., Science and Religion : Are the Compatible?, Prometheus Books, 2003
৫১ Edward J. Larson, Leading scientists still reject God, Nature, Vol. 394, No. 6691, p. 313 (1998), Macmillan Publishers Ltd.; online : http://www.stephenjaygould.org/ctrl/news/file002.html
৫২ Francis S. Collins, The Language of God : A Scientist Presents Evidence of Belief, New York : Free Press, 2006
৫৩ Fallacy of Fine-Tuning: Why the Universe Is Not Designed for Us, Prometheus Books, 2011
৫৪ The Cold Big-Bang Cosmology as a Counter-example to Several Anthropic Arguments.
৫৫ John Allen Paulos, Irreligion : A Mathematician Explains why the Arguments for God Just Don’t Add Up, Hill and Wang, 2009। পৃষ্ঠা ৯০।
৫৬ John Allen Paulos, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা নং ১১
৫৭ ডারউইন দিবসে রিচার্ড ডকিন্স পরিচিতি, অভিজিৎ রায়, মুক্তমনা।
৫৮ Natural Theology, or Evidence of Existence and Attributes of the Deity, collected from the Appearances of Nature, London: Halliwell, 1802
৫৯ Keith Stewart Thomson, Before Darwin : Reconciling God and Nature, New Haven and London: Yale University Press, 2005, পৃষ্ঠা নং ২০
৬০ ইরতিশাদ আহমদ, বিবর্তনের সাক্ষ্যপ্রমাণ-১ (জেরি কোসেন-এর ‘বিবর্তন কেন বাস্তব’ অবলম্বনে), মুক্তমনা।
৬১ Charles Darwin, The Origin of Species by Means of Natural Selection,London: John Murray, 18591
৬২ Michael Shermer,Why People Believe Weird Things : Pseudoscience, Superstition, and Other Confusions of Our Time, W.H. Freeman & Company, 1998, তৃতীয় অধ্যায়, পৃষ্ঠা নং ১৪০]
৬৩ Victor J. Stenger, God: The Failed Hypothesis : How Science Shows That God Does Not Exist, Prometheus Books, 2007, পৃষ্ঠানং ৪৯
৬৪ এক বিবর্তনবিরোধীর প্রত্যুত্তরে, অভিজিৎ রায়, মুক্তমনা।
৬৫ ভ্রান্ত ধারণা, বিবর্তন কখনো বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে। এই দাবির উত্তর, মুক্তমনা বিবর্তন আর্কাইভ, http ://www.mukto-mona.com/evolution
৬৬ Victor J. Stenger, God : The Failed Hypothesis : How Science Shows That God Does Not Exist, Prometheus Books, 2007, পৃষ্ঠা নং ৫১
৬৭ Richard Dawkins, The Blind Watchmaker : Why the Evidence of Evolution reveals a Universe Without Design, London, New York, : Norton, 1987 পৃষ্ঠা নং ৯৩
৬৮ Kenneth R. Miller, Lifes Grand Design, পৃষ্ঠা নং ২৪-৩২
৬৯ Richard Dawkins, Climbing Mount Improbable, W. W. Norton & Company,1997, The Fortyfold Path to Enlightenment’ অধ্যায়।
৭০ R. D. Fernald, ‘Evolution of Eyes, Current Opinion in Neurobiolog নং ৪৪৪-৫০
৭১ জাকির নায়েকের মিথ্যাচার : প্রসঙ্গ বিবর্তন। খান মুহাম্মদ (শিক্ষানবিস), মুক্তমনা।
৭২ বন্যা আহমেদ, বিবর্তনের পথ ধরে (অবসর প্রকাশনী, ঢাকা)। অধ্যায় ‘ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন : সৃষ্টিতত্বের বিবর্তন।
৭৩ বন্যা আহমেদ, বিবর্তনের পথ ধরে, পূর্বোক্ত।
৭৪ H. J. Muller, ‘Recersibility in Evolution Considered from the Standpoint of Genetics Biological Review 14 (1939) : 261- ৪০. সৃষ্টিবাদীরা একটি কথা প্রায়ই বলে থাকেন, আজ অবধি কোনো বিবর্তন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার লাভ করেন নি, যা মিথ্যা।
৭৫ Sean D. Hooper and Otto G. Berg, On the Nature of Gene Innovation : Duplication Patterns in Microbial Genomes, Mol. Biol. Evol. 20(6):945 954. 2003
৭৬ Lynch M, Conery JS., The evolutionary fate and consequences of duplicate genes, Science 290, 1151-1155.
৭৭ Doriit, review of Darwin’s Black Box; Miller, Finding Darwin’s God; Perakh, Unintelligent Design; Davis Ussery, ‘Darwin’s Transparent Box : The Biochemical Evidence for Evolution.’ in Young and Edis, Why Intelligent Design Fails, চতুর্থ অধ্যায়।
৭৮ Stephen J. Gould, The Pandas Thumb (New York: Norton, 1980), ১৯ ৩৪ পৃষ্ঠা
৭৯ Matt Young, Grand Designs and Facile Analogies : Exposing Behe’s Mousetrap and Dembski’s Arrow’, Why Intelligent Design Fails : A Scientific Critique of the New Creationism, Rutgers University Press (June 25, 2004)
৮০ Dembski, ‘The Design Inference’, ‘Intelligent Design’, ‘The Design Inference.’
৮১ পূর্বোক্ত
৮২ ৬ পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৮-৩১
৮৩ এই বিষয়ে নতুন লেখার জন্য পড়ে দেখা যেতে পারে, Why Intelligent Design Fails Gishlack, Shanks 18 Karsai; Hurd, Shallit এবং Elsberry; Perakh in Young এবং Edis এর লিখিত অধ্যায়গুলো।
৮৪ Jerry A. Coyne, Why Evolution is True?, Viking Adult, 20 ৮৬।
৮৫ পূর্বোক্ত বই, একই পৃষ্ঠা।
৮৬ সায়েন্টিফিক এমেরিকান, মার্চ ২০০১ সংখ্যা
৮৭ অভিজিৎ রায়, মানব মস্তিষ্কের আনইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন, মুক্তমনা, মে ২১, ২০১২
৮৮ A. Skybreak, The Science of Evolution and The Myth of Creationism, Insight Press, Illinois, USA
৮৯ অনন্ত বিজয় দাশ, মহাপ্লাবনের বাস্তবতা: পৌরাণিক অতিকথন বনাম বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, মুক্তমনা
৯০ Michael Shermer,Why People Believe Weird Things : Pseudoscience, Superstition, and Other Confusions of Our Time, W.H. Freeman & Company, 1998, পৃষ্ঠা নং ১৩০
৯১ একই বই, একই পৃষ্ঠা।
৯২ ডিসকভারি ইন্সটিটিউট এর ওয়েবসাইট।
৯৩ Phillip Ball, The Self- Made Tapestry: Pattern Formation in Nature, New York, Oxford : Oxford University Press, 2001
৯৪ Jhon Gribbon, Deep Simplicity : Bringing Order to Chaos and Complexity, New York : Random House, 2004
৯৫ Ball, The Self-Made Tapestry, Oxford University Press, 1999, TOT 9951 ১০৫- ১০৭
৯৬ S. Douady and Y. Couder, ‘Phyllotaxis as a Physical Self- Organized Growth Process’, Physical Review Letters 68 (1992): 2098
৯৭ Victor J. Stenger, God: The Failed Hypothesis : How Science Shows That God Does Not Exist, Prometheus Books
৯৮ Stuart Kauffman, At Home in The Universe : The Search for the Laws of Self- Organization and Complexity, New York and Oxford: Oxford University Press, 1995
৯৯ J. Craig Venter, Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically Synthesized Genome, Science DOI: 10.1126/science.1190719
১০০ অভিজিৎ রায়, আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, অঙ্কুর, ২০০৬ দ্র.
১০১ Huxley T.H. the animals which are most nearly intermediate between birds and reptiles. Geol. Mag. 5, 357–65; Annals & Magazine of Nat Hist 2, 66– 75; Scientific Memoirs 3,3-13, 1968.
১০২ পরে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে স্থানান্তরিত; লন্ডন স্পেসিমেন হিসেবে গণ্য।
১০৩ বার্লিন স্পেসিমেন হিসেবে গণ্য
১০৪ ম্যাক্সবার্গ স্পেসিমেন হিসেবে গণ্য
১০৫ Charig, A.J.; Greenaway, F.; Milner, A.N.; Walker, C.A.; and Whybrow, P.J., ‘Archaeopteryx is not a forgery’. Science 232 (4750): 622–626, 1986
১০৬ Wellnhofer P., A New Speciment of Archaeopteryx, Science 240, 1790, 1988.
১০৭ Tim Berra, Evolution and the Myth of Creationism : A Basic Guide to the Facts in the Evolution Debate, Stanford University Press, 1990, p41.
১০৮ Elliot Meyerowitz of Caltech quoted by Gail Vines, New Scientist 2 Dec 2000 p36-39.
১০৯ Hoyle Fred, The Intelligent Universe. New York : Holt, Rinehart and Winston, 1983, pp. 18-19
১১০ Fred Hoyle and Chandra Wickramasinghe, Lifecloud : The Origin of Life in the Universe, 1978, p.15-16 1
১১১ Fred Hoyle and Chandra Wickramasinghe, Our Place in the Cosmos, 1993, p.14
১১২ Derek Gatherer, The Open Biology Journal, 2008, 1, 9–20, Finite Universe of Discourse : The Systems Biology of Walter Elsasser (1904–1991)
১১৩ Why Evolution Isn’t Chance
http ://www.ebonmusings.org/evolution/evonotchance.html
১১৪ বন্যা আহমেদ, বিবর্তনের পথ ধরে, অবসর প্রকাশনী, ২০০৭
১১৫ Nilsson, D.-E., and S. Pelger. 1994. A pessimistic estimate of the time required for an eye to evolve. Proc. Roy. Soc. Lond. B 256:53-58.
১১৬ অভিজিৎ রায় এবং ফরিদ আহমেদ, মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে, অবসর, ২০০৭
১১৭ Haiti earthquake survivor Evan Muncie trapped under rubble for 27 days, Times Online, February 10, 2010,
http ://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article702116 8.ece
১১৮ Richard Dawkins, The Blind Watchmaker : Why the Evidence of Evolution Reveals a Universe without Design, W. W. Norton & Company, 1996, page 49.
১১৯ অভিজিৎ রায়, বিবর্তনের সহজ পাঠ,যুক্তি, সংখ্যা ৩, জানুয়ারি ২০১০; এছাড়া অনলাইনে পড়ুন, এক বিবর্তনবিরোধীর প্রত্যুত্তরে
: http://mukto-mona.com/banga_blog/?p=936
১২০ http://www.youtube.com/watch?v=OvE1110c0lw,
১২১ John Rennie, Scientific American, July 2002, ‘15 Answers to Creationist Nonsense’, page 81
১২২ ডকিন্সের বায়োমর্ফ সম্বন্ধে জানতে হলে এই ভিডিওটি দেখা যেতে পারে
httpv ://www.youtube.com/watch?v=4ThaHhIkYAC
১২৩ উদাহরণ হিসেবে দেখা যেতে পারে, http ://www.viewingspace.com/genetics_culture/pages_ genetics_culture/gc_w05/somm_mign_webarchive/lifespaciesII/LifeAni m.gif ইত্যাদি
১২৪ War of Weasels : An Evolutionary Algorithm Beats Intelligent Design, Skeptical Inquirer, Vol 34, No. 3.
১২৫ Ian Musgrave, Lies, Damned Lies, Statistics, and Probability of Abiogenesis Calculations, TalkOrigins Archive.
১২৬ Oparin, A. I., Origin of Life. New York : Dover, 1952
১২৭ Haldane JBS, The Origins of Life, New Biology, 16, 12–27 (1954).
১২৮ Miller, Stanley L., ‘Production of Amino Acids Under Possible Primitive Earth Conditions Science 117 (3046):528, 1953
১২৯ Miller, Stanley L.; Harold C. Urey, ‘Organic Compound Synthesis on the Primitive Earth’. Science 130 (3370): 245, 1959
১৩০ Fox, S. W. How did life begin? Science 132 : 200-208, 1960.
১৩১ Fox, S. W. and K. Dose. Molecular Evolution and the Origin of Life, Revised ed. New York : Marcel Dekker, 1977.
১৩২ Cairn-Smith, A. G. Seven Clues to the Origin of Life, Cambridge University Press, 1985.
১৩৩ de Duve, Christian, The beginnings of life on earth. American Scientist 83 :428-437, 1995
১৩৪ Russell, M. J. and A. J. Hall, The emergence of life from iron monosulphide bubbles at a submarine hydrothermal redox and pH front. Journal of the Geological Society of London 154 : 377-402, 1997.
১৩৫ Wächtershäuser, Günter, Life as we don’t know it. Science 289 : 1307 1308, 2000.
১৩৬ Smith, J. V., F. P. Arnold Jr., I. Parsons, and M. R. Lee. 1999. Biochemical evolution III : Polymerization on organophilic silica-rich surfaces, crystal chemical modeling, formation of first cells, and geological clues. Proceedings of the National Academy of Science USA 96(7): 3479-3485. 137।
১৩৭ Huber, Claudia, Wolfgang Eisenreich, Stefan Hecht and Günter Wächtershäuser. 2003. A possible primordial peptide cycle. Science 301 : 938-940
১৩৮ Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically Synthesized Genome’. science magazine., Published Online May 20, 2010, Science DOI : 10.1126/science.1190719
১৩৯ Stuart Kauffman, At Home in The Universe : The Search for the Laws of Self- Organization and Complexity, New York and Oxford : Oxford University Press, 1995
Phillip Ball, The Self- Made Tapestry : Pattern Formation in Nature, New York, Oxford: Oxford University Press, 2001
১৪০ John Maynard Smith, The Problems of Biology, p.49. (1986), ISBN 0-19 289198-7, ‘What is wrong with it? Essentially, it is that no biologist imagines that complex structures arise in a single step.
১৪১ George Johnson, Bright Scientists, Dim Notions NY Times, October 28, 2007
১৪২ Richard Dawkins, The God Delusion, Houghton Mifflin Harcourt; 2006, page 114
১৪৩ অভিজিৎ রায়, আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, অঙ্কুর প্রকাশনী (২০০৫, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৬)
১৪৪ John Allen Paulos, Irreligion : A Mathematician Explains why the Arguments for God Just Don’t Add Up, Hill and Wang, 2009, পৃষ্ঠা ৫
১৪৫ Richard Swinburne, The Existence of God, Oxford: Clarendon Press, 1979, পৃষ্ঠা নং ২২৯।
১৪৬ Conservation of energy was not immediately recognized but was already implicit in Newton’s laws of mechanics, Victor J. Stenger, God: The Failed Hypothesis : How Science Shows That God Does Not Exist, Prometheus Books, 2007, পৃষ্ঠা ১১২]
১৪৭ সাধারণভাবে ধারণা করা হয়ে থাকে যে, শুধু নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার মাধ্যমেই স্থিতি শক্তি থেকে গতি শক্তি বা গতি শক্তি থেকে স্থিতি শক্তিতে রূপান্তরের ঘটনা ঘটা সম্ভব। কিন্তু একই সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়াতেও এমনটা ঘটে। তবে ব্যাপার হলো, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় বিক্রিয়কের ভর খুব নগণ্য থাকে বিধায় বোঝা মুশকিল হয়।
১৪৮ Stephen W. Hawking, A Brief History of Time : From the Big Bang to Black Holes, New York: Bantam, 1988, পৃষ্ঠা নং ১২৯
১৪৯ ইনফ্লেশন বা স্ফীতিতত্বের আবির্ভাবের পর আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান খুব পরিষ্কারভাবেই আমাদের দেখিযেছে মহাবিশ্বে মোট শক্তির পরিমাণ শূন্য; মহাবিশ্বের মোট গতিশক্তি এবং মাধ্যাকর্ষণের ঋণাত্মক শক্তি পরস্পরকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। এর মানে হচ্ছে মহাবিশ্ব সৃষ্টির জন্য বাইরে থেকে আলাদা কোনো শক্তির প্রয়োজন হয় নি। সহজ কথায়, ইনফ্লেশন ঘটাতে যদি শক্তির নিট ব্যয় যদি শূন্য হয়, তবে বাইরে থেকে কোনো শক্তি আমদানি করার প্রয়োজন পড়ে না। অ্যালান গুথ এবং স্টেইনহার্ট। নিউ ফিজিক্স জার্নালে (১৯৪৯) দেখিয়েছেন, ইনফ্লেশনের জন্য কোনো তাপগতীয় কাজের দরকার পড়ে না। স্টিফেন হকিং তাঁর অতি সাম্প্রতিক গ্র্যান্ড ডিজাইন’ বইয়ে সুস্পষ্টভাবে মত প্রকাশ করেছেন যে, এই মহাবিশ্ব প্রাকৃতিকভাবেই শূন্য থেকে উদ্ভূত হয়েছে, কোনো অলৌকিক কিংবা অপার্থিব সম্বার হস্তক্ষেপ ছাড়াই।
১৫০ V.Faraoni 95 F. I. Cooperstock, ‘On the Total Energy of Open Friedmann- Robertson-Walker Universes’, Astrophysical Journal 587 (2003): 483-86
১৫১ মীজান রহমান এবং অভিজিৎ রায়, শূন্য থেকে মহাবিশ্ব, শুদ্ধস্বর, ২০১৫ (প্রকাশিতব্য)
১৫২ Alan Guth, The Inflationary Universe, New York: Addison-Wesley, 1997;
আরো দেখুন– Anthony Aguirre, How did Our Universe Come to be?, Astronomy’s 60 Greatest Mysteries, Sky and Telescope, 2013
১৫৩ চিত্রটির গাণিতিক ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে, Victor J. Stenger এর Has Science Found God? The Latest Results in the Search for Purpose in the Universe, Amherst, NY: Prometheus Books, 2003 বইয়ের appendix C, পৃষ্ঠা নং ৩৫৬-৫৭ তে।
১৫৪ Victor J. Stenger 95 Has Science Found God? The Latest Results in the Search for Purpose in the Universe, Amherst, NY: Prometheus Books, 2003, পৃষ্ঠা নং ৩৫১-৫৩।
১৫৫ এই লাইনটি আবারো একটু বিশদভাবে ব্যাখ্যার দাবি রাখে। সাধারণত পদার্থবিজ্ঞানের বইগুলোতে (যেমন শন ক্যারলের ‘From Eternity to Here: The Quest for the Ultimate Theory of Time’ বইটি দ্রষ্টব্য) বলা হয়ে থাকে মহাবিশ্ব শুরু হয়েছে খুব নিম্ন এনট্রপির অবস্থা থেকে। মনে হতে পারে যে উপরিউক্ত লাইনটি সেই বাস্তবতার পরিপন্থী। হ্যাঁ, নিম্ন এন্ট্রপি থেকে মহাবিশ্বের যাত্রা শুরুর ব্যাপারটা যেভাবে সাধারণ বইগুলোতে বলা হয় সেটা ভুল নয়, কিন্তু একই সাথে মহাবিশ্ব যাত্রা শুরু করতে পারে সর্বোচ্চ এনট্রপি অর্থাৎ কোয়ান্টাম স্কেলের চরম বিশৃঙ্খলা থেকেও, যাকে ‘কেওস’ নামে অভিহিত করা হয়। আর তারপর যখন থেকে মহাবিশ্ব প্রসারিত হতে শুরু করল, সর্বোচ্চ এনট্রপি বাড়তে থাকল প্রকৃত এন্ট্রপি থেকে দ্রুত হারে (প্রদত্ত গ্রাফ দ্রষ্টব্য)। সেজন্যই অধ্যাপক ভিক্টর স্টেঙ্গর তার ‘ডিফেন্ডিং দ্য ফ্যালাসি অব ফাইনটিউনিং শিরোনামের পেপারে বলেন, ‘A volume of space can have maximal entropy and still contain very low entropy as compared to the visible universe. Assume our universe starts out at the Planck time as a sphere of Planck dimensions. Its entropy will be as low as it can be. However, at the same time, a Planck sphere is akin to a black hole whose entropy is maximal for an object of the same radius. It is not logically inconsistent to be both low and maximum at the same time. In short, the universe could have started out in complete disorder and still produced organized structures. The reason is, as the universe expands its maximum allowed entropy grows with it so that order can form without violating the second law of thermodynamics.’
১৫৬ Stephen W. Hawking and Roger Penrose, ‘The Singularities of Gravitational Collapse and Cosmology,’ Proceedings of the Royal Society of London, series A, 314 (1970) : পৃষ্ঠা নং ৫২৯-৪৮
১৫৭ Dines D’Souza, What’s So Great About Christianity?,Washington, DC: Regnery, 2007, পৃষ্ঠা নং ১১৬
১৫৮ Dines D’ Souza, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৩
১৫৯ অনন্ত বিজয় দাশ, হারুন ইয়াহিয়া : চকচক করলেই সোনা হয় না, যুক্তি, সংখ্যা ৪, জুলাই ২০১৩
১৬০ যেমন, জাকির নায়েক তার একটি লেকচারে বলেছেন,
As far as Qur’an and modern Science is concerned, in the field of ‘Astronomy’, the Scientists, the Astronomers, a few decades earlier, they described, how the universe came into existence— They call it the ‘Big Bang’. And they said… ‘Initially there was one primary nebula, which later on it separated with a Big Bang, which gave rise to Galaxies, Stars, Sun and the Earth, we live in.’ This information is given in a nutshell in the Glorious Qur’an, in Surah Ambiya, Ch. 21, Verse No. 30, which says, ‘Do not the unbelievers see that the heavens and the earth were joined together, and we clove them asunder?’ Imagine this information which we came to know recently, the Qur’an mentions 14 hundred years ago.
১৬১ এ প্রসঙ্গে পড়ুন, এই বইটির ‘বিজ্ঞানময় কিতাব’ শিরোনামের অধ্যায়টি।
১৬২ Stephen W. Hawking, A Brief History of Time : From the Big Bang to Black Holes, New York: Bantam, 1988, পৃষ্ঠা ৫০
১৬৩ D’Souza, What’s So Great About Christianity?, Washington, DC: Regnery, 2007, পৃষ্ঠা ১২১
১৬৪ Stephen W. Hawking, A Brief History of Time: From the Big Bang to Black Holes, New York: Bantam, 1988, পৃষ্ঠা ৫০।
১৬৫ Stephen W. Hawking, পূর্বোক্ত।
১৬৬ Ravi K. Zacharias, The End of Reason : A Response to the New Atheist, Grand Rapids, MI: Zondervan, 2008, পৃষ্ঠা নং ৩১]
১৬৭ Andrei Linde, The Self-Reproducing Inflationary Universe, Scientific American, November, 1994
১৬৮ Victor J. Stenger, God and the Atom, Prometheus Books, 2013 169
১৬৯ E.P. Tryon, ‘Is the Universe a Vacuum Fluctuation?”, Nature 246 (1973): 396-97.
১৭০ আবদ্ধ মহাবিশ্বে মোট শক্তি যে শূন্য থাকে তা ট্রিয়নের সময়ই বিজ্ঞানীরা জানতেন। যেমন বিখ্যাত পদার্থবিদ এল ডি লান্ডাউ এবং ই এম লিফশিৎস ১৯৬২ সালে লেখা ‘The Classical Theory of Fields’ পাঠ্য বইয়ে এটি ব্যাখ্যা করেছিলেন। কিন্তু ট্রিয়ন সম্ভবত এই উৎস সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না।
১৭১ Alexander Vilenkin, ‘Creation of Universe from Nothing” Physics letters 117B (1982) 25-28
১৭২ Alex Vilenkin, Many Worlds in One: The Search for Other Universes, Hill and Wang, 2006
১৭৩ James B. Hartle and Stephen W. Hawking, ‘Wave Function of the Universe,” Physical Review D28, 2960-75, 1983
১৭৪ Stephen William Hawking, The Universe in a Nutshell, Bantam, 2001
১৭৫ ‘দ্য গ্যান্ড ডিজাইন’— স্টিফেন হকিং [অধ্যায় ৬] (অনুবাদ তানভীরুল ইসলাম)
১৭৬ ভিকটর স্টেঙ্গরের এই বাইভার্স মডেলের সাথে পরিচিত হতে হলে তাঁর The Fallacy of Fine-Tuning: Why the Universe Is Not Designed for Us (Prometheus Books, 2011) অথবা Timeless Reality : Symmetry, Simplicity, and Multiple Universes (Prometheus Books, 2000) দ্রষ্টব্য।
১৭৭ Victor J. Stenger, The Comprehensible Cosmos : Where Do the Laws of Physics Come From?, Amherst, NY: Prometheus Books, 2006, পৃষ্ঠা নং ৩১২-১৯।
১৭৮ Victor J. Stenger, ‘A Scenario for a Natural Origin of Our Universe, ‘Philo 9, no 2 (2006): 93- 102]
১৭৯ Victor J. Stenger, The New Atheism, Amherst, NY : Prometheus Books, 2006, পৃষ্ঠা নং ১৭১
১৮০ Stephen Hawking and Leonard Mlodinow, The Grand Design, Bantam, 2010
১৮১ Lawrence M. Krauss, A Universe from Nothing: Why There Is Something Rather than Nothing, Free Press, 2012.
১৮২ এ বিষয়ে বাংলায় পড়তে চাইলে মীজান রহমান ও অভিজিৎ রায়, ‘শূন্য থেকে মহাবিশ্ব’, শুদ্ধস্বর, ২০১৫ (প্রকাশিতব্য) দ্রঃ
১৮৩ Elbert, Jerome W, Are Souls Real? 2000, Prometheus Books.
১৮৪ Kurtz, Paul, Science and Religion : Are They Compatible?, 2003, Prometheus Books
১৮৫ অভিজিৎ রায় এবং ফরিদ আহমেদ, মহাবিশ্বে প্রাণ ও বুদ্ধিমত্তার খোঁজে, অবসর, ২০০৭
১৮৬ Zimmer, Carl, Soul Made Flesh : The Discovery of the Brain-and How It Changed the World, 2004, New York : Free Press.
১৮৭ Bremmer, Jan N., The Early Greek Concept of the Soul, Princeton University Press; Reissue edition, 1987.
১৮৮ Elbert, Jerome W, Are Souls Real? 2000, Prometheus Books.
১৮৯ Gora, God and Soul, Atheism : Questions and Answers, Atheist Center, Vijayawada.
১৯০ Bremmer, Jan N., The Early Greek Concept of the Soul, Princeton University Press; Reissue edition, 1987.
১৯১ Swin, Tony, A place for Strangers : Towards a history of Australian Aboriginal Being, 1993, Cambridge University Press.
১৯২ প্রবীর ঘোষ, অলৌকিক নয়, লৌকিক (প্রথম ও পঞ্চম খণ্ড), দে’জ পাবলিশিং, ২০০৩।
১৯৩ Bremmer, Jan N., The Early Greek Concept of the Soul, Princeton University Press; Reissue edition, 1987.
১৯৪ Kurtz, Paul, Science and Religion : Are They Compatible?, 2003, Prometheus Books
১৯৫ অপরাজিত বসু, প্রাণের রহস্য সন্ধানে বিজ্ঞান, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৯৯।
১৯৬ শহিদুল ইসলাম, বিজ্ঞানের দর্শন (প্রথম খণ্ড), শিক্ষাবার্তা প্রকাশনা, ২০০৫
১৯৭ শহিদুল ইসলাম, পূর্বোক্ত
১৯৮ অভিজিৎ রায় এবং ফরিদ আহমেদ, পূর্বোক্ত
১৯৯ প্রবীর ঘোষ, অলৌকিক নয়, লৌকিক (প্রথম ও পঞ্চম খণ্ড), দে’জ পাবলিশিং, ২০০৩
২০০ Francis, Astonishing Hypothesis : The Scientific Search for the Soul, 1995, Scribner.
২০১ Rebecca Skloot, The Immortal Life of Henrietta Lacks, Crown, 2010
২০২ Clark, William R, Sex and the Origins of Death, 1998, Oxford University Press, USA.
২০৩ Steven Laureys, Eyes Open, Brain Shut; May 2007; Scientific American Magazine, May 2007.
২০৪ Stone Alex, Suspended Animation : Is Induced hibernation the key to surviving a trip to the ER? Discover, May 2007.
২০৫ Rationally speaking, Does the soul weigh 21 grams? March 08, 2007
২০৬ Bosveld, Jane, Soul Search : Can science ever decipher the secrets of the human soul? Discover, June 2007
২০৭ Robert Todd Carroll, Near-death experience (NDE), Skeptic’s Dictionary, Last updated 12/03/07, http://skepdic.com/nde.html
২০৮ Avijit Roy, Construction of Physics-based brain atlas and its application, PHD Thesis, NUS, 2007
২০৯ Blackmore, Susan, Consciousness : A Very Short Introduction (Very Short Introductions) (Paperback), 2005, Oxford University Press.
২১০ Roger Penrose, The Emperor’s New Mind, Oxford University Press, USA; New Paperback edition, 2002.
২১১ Blackmore, Susan, Dying to Live : Near-Death Experiences, 1993, Prometheus Books.
২১২ http://www.issc-taste.org/index.shtml
২১৩ S. J. Blackmore and T. S. Troscianko., The physiology of the tunnel.
২১৪ Journal of Near-Death Studies, 8:15-28, 1989 Susan Blackmore, Near-Death Experiences : In or out of the body? Skeptical Inquirer 1991, 16, 34-45.
২১৫ Bressloff, Paul C., Jack D. Cowan, Martin Golubitsky, Peter J. Thomas, and Matthew C. Wiener. What Geometric Visual Hallucinations Tell Us About the Visual Cortex. Neural Computation. Vol. 14, No. 3, 473-491, 2002
২১৬ David Biello, Searching for God in the Brain; Scientific American Mind, October/November 2007
২১৭ V. S. Ramachandran and Sandra Blakeslee, Phantoms in the Brain : Probing the Mysteries of the Human Mind, Harper Perennial, 1999.
২১৮ দীক্ষক দ্রাবিড়, মানুষের পয়গম্বর হয়ে ওঠার সুলুকসন্ধান, মুক্তান্বেষা, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা।
২১৯ John Horgan, The God Experiments : Five researchers take science where it’s never gone before, Discover, December, 2006
২২০ Robert Hercz, The God Helmet, Saturday Night Magazine, p 40-46, 2002
২২১ Robert Hercz, The God Helmet, Saturday Night Magazine, p 40-46, 2002
২২২ Crick, Francis, Astonishing Hypothesis : The Scientific Search for the Soul, 1995, Scribner.
২২৩ আমেরিকান ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ এন্ড হিউম্যান সার্ভিসের দেওয়া তথ্য থেকে জানা গেছেএকটি মৃতদেহের অন্তত: পঞ্চাশটি অঙ্গকে নাকি নানাভাবে অন্য মানুষের কাজে লাগানো যায়। (অভিজিৎ রায়, মরণোত্তর দেহদান– মানবতার জন্য হোক আপনার সর্বশেষ দান, মুক্তমনা, আগস্ট ২২, ২০১২)।
২২৪ আরজ আলী মাতুব্বর রচনা সমগ্র, পাঠক সমাবেশ।
২২৫ অভিজিৎ রায়, একজন বেলাল মোহাম্মদ এবং তাঁর মরণোত্তর দেহদান, মতামত-বিশ্লেষণ, বিডিনিউজ২৪, আগস্ট ১৯,২০১৩
২২৬ Volume 4, Book 54, Number 421 : Narrated Abu Dhar :
The Prophet asked me at sunset, ‘Do you know where the sun goes (at the time of sunset)?’ I replied, ‘Allah and His Apostle know better.’ He said, ‘It goes (i.e. travels) till it prostrates Itself underneath the Throne and takes the permission to rise again, and it is permitted and then (a time will come when it will be about to prostrate itself but its prostration will not be accepted, and it will ask permission to go on its course but it will not be permitted, but it will be ordered to return whence it has come and so it will rise in the west. And that is the interpretation of the Statement of Allah :
And the sun Runs its fixed course For a term (decreed), that is The Decree of (Allah) The Exalted in Might, The All-Knowing.’ (36.38) Volume 6, Book 60, Number 326 : Narrated Abu Dharr : Once I was with the Prophet in the mosque at the time of sunset. The Prophet said, ‘O Abu Dharr! Do you know where the sun sets?’ I replied, ‘Allah and His Apostle know best.’ He said, ‘It goes and prostrates underneath (Allah’s) Throne; and that is Allah’s Statement : ‘And the sun runs on its fixed course for a term (decreed). And that is the decree of All-Mighty, the All-Knowing….’ (36.38) Volume 6, Book 60, Number 327 : Narrated Abu Dharr : I asked the Prophet about the Statement of Allah : ‘And the sun runs on fixed course for a term (decreed),’ (36.38) He said, ‘Its course is underneath ‘Allah’s Throne.’ (Prostration of Sun trees, stars. mentioned in Qur’an and Hadith does not mean like our prostration but it means that these objects are obedient to their Creator (Allah) and they obey for what they have been created for).
২২৭ জাকির নায়েকঃ কোন কোন ইসলামিস্ট সাম্প্রতিককালে ‘দাহাহা’ শব্দের অর্থ করার চেষ্টা করেছেন, ‘উট পাখির ডিম’ বা ‘উট পাখির ডিমের মতো আকৃতির। তারা বলেন, এই আয়াতে দাহাহা দ্বারা ‘বিস্তৃত করা বোঝানো হয় নি (যদিও পাঠক থোল করলেই দেখবেন যে, অন্য সকল স্থানে কিন্তু বিস্তৃত করাই বোঝানো হয়েছে, এবং ইউসুফ আলী কিংবা পিকথালের অনুবাদে expanding অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে)। এর দ্বারা নাকি বোঝানো হয়েছে, গোলাকার তথা উট পাখির ডিমের মতো করে তৈরি করা। কারণ হিসেবে এই ইসলামিক স্কলাররা। বলছেন, দাহাহা শব্দের মূল হলো ‘দুহিয়া’ যার অর্থ উট পাখির ডিম। এটা যে কষ্টকল্পিত আর জোড়াতালি ব্যাখ্যা তা না বললেও বোধ হয় চলবে। এখানে ‘দাহাহা’র সাথে উট পাখির ডিমের সম্পর্ক কোনোভাবেই করা যায় না। আরবি অভিধান ঘাঁটলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ডিমের আরবি হলো আল বাইজা, দুহিযা/দাহাহা নয়। তারপরও অনেকে ডিম নিয়ে পড়ে থাকতে চান, আর মানুষকে প্রতারিত করেন। যদি ডিমের ব্যাপারটি সঠিক বলে ধরেও নেই, তারপরেও তাদের যুক্তি ধোপে টেকে না। পৃথিবীর আকৃতি আসলে ডিমের মতো না। এমনকি স্কুলের ভূগোল বইয়েই পাওয়া যায় পৃথিবীর আকৃতি অনেকটা কমলালেবুর মতো- উত্তর দক্ষিণে খানিকটা চাঁপা। এধরণের আকৃতিকে বলে oblate (বিষুব বরাবর প্রসারিত)। আর অন্য দিকে ডিমের আকৃতি উত্তর দক্ষিণে ছুঁচালো, কারণ ডিম হলো prolate আকৃতির (মেরু বরাবর প্রসারিত)। এ প্রসঙ্গে আরও জানার জন্য উইকি ইসলাম থেকে দেখুন
The Flat Earth, http ://wikiislam.net/wiki/The_Flat_Earth
২২৮ এ প্রসঙ্গে আরও পড়ুন, খান মুহাম্মদ (শিক্ষানবিস), ইসলামী বিজ্ঞানের পৌরাণিক কাহিনি, মুক্তমনা।
২২৯ T.J. de Boer তার History of Philosophy in Islam (1904) বইয়ে বলেছেন যে, পৃথিবীকে গোলাকার হিসবে বিবেচনা করে হাইখাম অপবিত্র নাস্তিকের প্রতাঁকে (unhappy symbol of impious Atheism) পরিণত হয়ে গিয়েছিলেন, এবং তার কাজকর্ম জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয়। এছাড়া Bradley Steffens এর Ibn al-Haytham : First Scientist বইয়েও। হাইথামের পান্ডুলিপি পোড়ানোর উল্লেখ পাওয়া যায়।
২৩০ যদিও ফতোয়াটি নিয়ে কিছুটা বিতর্ক আছে, কারণ শেখ আবদেল আজিজ ইবন বাজ পরে ফতোয়া দেওয়ার ব্যাপারটি অস্বীকার করেন। কিন্তু এখনো অন্তত তিনটি জায়গায় ফতোয়াটির উল্লেখ পাওয়া যায়[কার্ল সাগানের ‘The Demon-Haunted World (১৯৯৬ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৩২৫), অধ্যাপক পারভেজ হুদোভযের_Islam and Science : Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality (TOT 8)) এবং New York Times এর 1995 সালে প্রকাশিত Yousef M. Ibrahim এর প্রবন্ধ_Muslim Edicts take on New Force (The New York Times, February 12, 1995)
২৩১ বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন[The Flat-out Truth : The idea of a spinning globe is only a conspiracy of error that Moses, Columbus, and FDR all fought… http://www.lhup.edu/~dsimanek/fe-scidi.htm
২৩২ বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন[The International Square Earth Society,
http://pw1.netcom.com/~rogermw/square_earth.html
২৩৩ 1) Narrated Anas : Some people from the tribe of ‘Ukl came to the Prophet and embraced Islam. The climate of Medina did not suit them, so the Prophet ordered them to go to the (herd of milch) camels of charity and to drink, their milk and urine (as a medicine). Sahih Bukhari 8:82:794
2) Anas b. Malik reported that some people belonging to the tribe) of ‘Uraina came to Allah’s Messenger (may peace be upon him) at Medina, but they found its climate uncongenial. So Allah’s Messenger (may peace be upon him) said to them : If you so like, you may go to the camels of Sadaqa and drink their milk and urine. They did so and were all right. Sahih Muslim 16:4130
3) ‘A tradtionalist told me from one who had told him from Muhammad b. Talha from Uthman v. Abdul-Rahman that in the raid of Muharib and B. Thalaba the apostle had captured a slave called Yasar, and he put him in charge of his milch-camels to shepherd them in the neighborhood of al Jamma. Some men of Qays of Kubba of Bajila came to the apostle suffering from an epidemic and enlarged spleens, and the apostle told them that if they went to the milch camels and drank their milk and their urine they would recover, so off they went. From The Sirat Rasul Allah ( The Life of The Prophet of God), by Ibn Ishaq pages 677-678
২৩৪ আসলে কোরআনে কেন আকাশ ও পৃথিবী একসাথে মিশে থাকার কথা আছে তা সহজেই অনুমেয়। সেসময় প্যাগানসহ মধ্যপ্রাচ্যের অনেক গোত্রের উপকথা এবং লোককথাতেই আকাশ আর পৃথিবী মিশে থাকার আর হরেক রকমের দেব-দেবী দিয়ে পৃথক করার কথা বলা ছিল। যেমন মিশরের লোককথায় ‘গেব’ নামের এক দেবতা ছিলেন যিনি ছিলেন মৃত্তিকার দেবতা। এই গেবকে তার মা এবং বোন (আসমানের দেবী) থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ফলেই আকাশ আর পৃথিবী একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। আবার, সুমেরীয় উপকথা গিলগামেশের কাহিনিতেও আসমানের দেবী ‘অ্যান’কে মৃত্তিকার দেবতা ‘কী এর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলার কথা বলা আছে। এ সমস্ত উপকথা থেকে প্যাগান রেফারেন্সগুলো বাদ দিলে যা থাকবে, তা কোরআনেরই কাহিনি।
২৩৫ এ প্রসঙ্গে পড়ুন, অভিজিৎ রায়, অনন্ত মহাবিশ্বের সন্ধানে, সচলায়তন
২৩৬ Self Reproducing Inflationary Universe, Andrei Linde, Scientific American, 1998
২৩৭ Aparthib Zaman, Mixing Science with Religion, Mukto-Mona
২৩৮ http://www.submission.org/quran/app1.html
২৩৯ কাজী জাহান মিয়া, আল-কোরআন দ্য চ্যালেঞ্জ (মহাকাশ পর্ব ১), প্রকাশক : নাহরীন পারভীন, রায়ের বাজার, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ১৭-২৯
২৪০ ড. খন্দকার আব্দুল মান্নান, কম্পিউটার ও আল কোরআন, প্রকাশনায় : ইশায়াতে ইসলাম কুতুবখানা, মিরপুর, ঢাকা, পঞ্চম মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০০৩।
২৪১ হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, কোরআন শরীফ : সহজ সরল বাংলা অনুবাদ, আল কোরআন একাডেমী লন্ডন, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০২।
২৪২ কোরআনের সাংখ্যিক মাহাত্ম্য : ভিন্নমত, রায়হান আবীর
২৪৩ পুরো উপন্যাস পাওয়া যাবে এখানে :
http //www.spinelessbooks.com/gadsby/index.html
২৪৪ কোরআনের ‘মিরাকল ১৯’-এর উনিশ-বিশ! সৈকত চৌধুরী এবং অনন্ত বিজয় দাশ, মুক্তমনা বাংলা ব্লগ পিডিএফ লিংক-
http://www.mukto mona.com/Articles/ananta/nineteen_Ananta_soikot.pdf
২৪৫ কোরআনের ‘মিরাকল ১৯’-এর উনিশ-বিশ! সৈকত চৌধুরী এবং অনন্ত বিজয় দাশ, মুক্তমনা বাংলা ব্লগ
পিডিএফ লিংক। http ://www.mukto mona.com/Articles/ananta/nineteen_Ananta_soikot.pdf
২৪৬ বিস্তারিত তথ্যের জন্য পাঠকেরা পড়ুন অধ্যাপক ভিকটর স্টেঙ্গরের ‘In The Name Of The Omega Point Singularity’ (Free Inquiry 27. No.5 August/September 2007); এবং ডঃ লরেন্স ক্রাউসের ‘More dangerous than nonsense’ (New Scientist, 12 May 2007)
২৪৭ সাদ কামালী এবং অভিজিৎ রায় (সম্পাদনা), স্বতন্ত্র ভাবনা, চারদিক, ২০০৮
২৪৮ Karen Armstrong, The Battle for God, Ballantine Books, 2001; ক্যারেন আর্মস্ট্রং তাঁর ‘Battle for God’ বইয়ে বলেছেন, মানুষের চিন্তাধারা অনাদিকাল থেকেই বিকশিত হয়েছে পরিষ্কার দুটি ধারায়। এর একটি হচ্ছে ‘মিথোস’ এবং অপরটি ‘লোগোস’। মিথোস এসেছে ইংরেজি ‘মিথ’থেকে, আরও গভীরে গেলে পাওয়া যাবে ‘musteion] মিথের মূল প্রতিশব্দগুলো হলো mystery এবং mysticism, যা প্রকাশ করে রহস্যময়তা, দুজ্ঞেতা এবং অতীন্দ্রিয়তাকে। ক্যারেন আর্মস্ট্রং-এর চোথে মিথ হচ্ছে কতকগুলো রীতি-নীতি, আচার অনুষ্ঠান ও সংস্কারাযেগুলোর কোনো যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ কথনো পাওয়া যায় না। এগুলো মানব মনে জায়গা করে নিয়েছে স্রেফ কতকগুলো বিশ্বাসের কাঁধে ভর করে। আর আর্মস্ট্রং গ্রিক শব্দ লোগোসকে বর্ণনা করেছেন ‘যুক্তি গ্রাহ্য’, ‘প্রমাণসাপেক্ষ’, বিজ্ঞানভিত্তিক’ শব্দ ক’টির সাহায্যে। তিনি বলেন আধুনিক বিশ্বে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি, প্রগতি আর উন্নয়নের মূলে রয়েছে। ‘লোগোস–যা জ্ঞান ও যুক্তির মাপকাঠিতে প্রকৃত বাস্তবতার পরিচায়ক। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন, লেখকের কথা, আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, অভিজিৎ রায়, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৫]
২৪৯ ‘The religions of the world … have laid claim to the role of arbiters of human behavior. They insist that they have the right to tell the rest of us what is right and what is wrong because they have a special pipeline to the place where right and wrong are defined–in the mind of God.’, see ‘Do Our Values Come from God?, The Evidence Says No’, Victor stinger,
২৫০ বার্ট্রান্ড রাসেল, আমি কেন ধর্মবিশ্বাসী নই, ভাষান্তর : অরিন ভাদুড়ি, দীপায়ন, ২য় সংস্করণ, জানুয়ারি ২০০৪
২৫১ ‘Religion is an insult to human dignity. With or without it you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion.’; Steven Weinberg, In a speech given in Washington, DC, on April 1999.
২৫২ নাস্তিকতার সংজ্ঞা, সুমন তুরহানা দেশ ৪ নভেম্বর, ২০০২।
২৫৩ ‘ধর্ম যেহেতু ব্যক্তিগত ব্যাপার তাই ধর্মনিরপেক্ষ দেশে ধর্মীয় পরিচিয় জানানো জরুরি নয় বলে ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদীরা মনে করে। কিন্তু সমস্যা হলো, যারা কোনো ধর্ম মানেন না তারা চাকুরি বা শিক্ষার ক্ষেত্রে কলামটা খালি রাখতে চাইলেও অতীতে আপত্তি উঠেছে নানা জায়গায়। এমনকি ফর্ম বাতিল করা হয়েছে অসম্পূর্ণ বলে। সেই সময় বহু মানুষ দ্বারস্থ হয় ভারতীয় মানবতাবাদী সমিতির এই সময় প্রথম এই সমিতি Humanists’ Association of India সক্রিয় হয় মানবতাকে ধর্ম হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে, সেটা ১৯৯২-৯৩ সালের দিকে। দেশের রাজনৈতিক নেতাদের কাছে ও সংবাদপত্রের দপ্তরে যোগাযোগ। করে ঘটনাটি জানানো হয়। যাতে একজন মানুষ নিজের ধর্ম ‘মানবতা’ বলতে পারে তার জন্য সরকারি কোনো নিয়ামাবলী বা গাইডলাইন আছে কিনা তা স্পষ্টভাবে জানতে চাওয়া হয়। উত্তরে সবাই বলেন যে এভাবে নতুন ধর্ম তৈরি করা সম্ভব নয়। তারপর মানবতাবাদী সমিতি সরাসরি চিঠি পাঠায় জাতিসংঘের অফিসে। উত্তর আসে দেরি না করেই। ইউএনও তাদের Human rights এবং Religious rights সংক্রান্ত যাবতীয় বই ও কাগজপত্র পাঠিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেয] ১৯৮১’-এর জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে রাষ্ট্রসংঘ ঘোষণা করেছে প্রতিটি মানুষের যেকোনো ধর্মমত গ্রহণ ও চর্চা করার স্বাধীন অধিকার আছে। তারপরই এই আইনি লড়াইতে যৌথভাবে নেমে পড়ে ভারতের। মানবতাবাদী সমিতি ও যুক্তিবাদী সমিতি। জাতিসংঘকে চিঠি দিয়ে জানানো হয় যে ভারত জাতিসংঘের সদস্য দেশের অন্যতম হওয়া সত্বেও প্রচলিত ধর্মের বাইরে অন্য ধর্মকে এখানে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। হিউম্যানিজম-কেও ধর্ম বলে স্বীকার করা হয় না। কিন্তু যেহেতু ইউএনও তার গাইডলাইন পাঠিয়ে দিয়েছে, আমরা ইউএনও-এর অন্তর্গত দেশ হিসেবে মনে করি মানবতা আমাদের ধর্ম হতে কোনো বাধা নেই। এবং আইনিভাবে এই ধর্মমতকে গ্রহণ করার অধিকার ভারতের নাগরিকেরা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। এই চিঠির প্রতিলিপি পাঠানো হয় রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, আইনমন্ত্রী, সংসদবিষয়ক মন্ত্রী ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও বিদেশি দূতাবাসগুলোতেও। তারপর ভারতের মানবতাবাদী সমিতির সহায়তায় কোর্টে গিয়ে affidavit করে দলে দলে ছেলেমেয়ে Humanism-কে ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করে (১৯৯৩-এর ১০ ডিসেম্বর)। বিস্তারিত তথ্যের জন্য দেখুন : মানুষের ধর্ম মানবতা, সুমিত্রা পদ্মনাভন, দুই বাংলার
২৫৪ যুক্তিবাদীদের চোখে ধর্ম, পুনঃ মুদ্রিত, মুক্তমনা দ্র.। 254 অলৌকিক নয়, লৌকিক, প্রথম খণ্ড, প্রবীর ঘোষ, দে’জ পাবলিশিং
২৫৫ ‘I criticized fundamentalists as well as religion in general. I don’t find any difference between Islam and Islamic fundamentalists. I believe religion is the root, and from the root fundamentalism grows as a poisonous stem. If we remove fundamentalism and keep religion, then one day or another fundamentalism will grow again. I need to say that because some liberals always defend Islam and blame fundamentalists for creating problems. But Islam itself oppresses women. Islam itself doesn’t permit democracy and it violates human rights. ‘One Brave Woman vs. Religious Fundamentalism, An Interview With Taslima Nasrin, Free Inquiry magazine, Volume 19, Number1, available online http://www.secularhumanism.org/library/fi/nasrin_19_1.html
২৫৬ কোরআন শরীফ (বঙ্গানুবাদ), মাওলানা খান মুহাম্মদ ইউসুফ আবদুল্লাহ, সোলেমানিয়া বুক হাউস।
২৫৭ প্রথম আলোর অক্টোবর ১৮, ২০০৫ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী খোদ বাংলাদেশেই ২৯ টি কিংবা তারও বেশি জঙ্গি সংগঠনের অস্তিত্ব রয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হল : জমিয়াতুল মুজাহিদিন, জাগ্রত মুসলিম জনতা, শাহাদাত-ই আল হিকমা, হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামি, শহীদ নসুরুল্লাহ আল আরাফাত বিগ্রেড, হিজবুত তাওহিদ, জামায়াত-ই ইয়াহিয়া, আল তুরাত, আল হারাত আল ইসলামিয়া, জামাতুল ফালাইয়া তাওহিদি জনতা, বিশ্ব ইসলামী ফ্রন্ট, জুমাতুল আল সাদাত, শাহাদাত-ই-নবুওয়ত, আল্লাহর দল, জইশে মোস্তফা বাংলাদেশ, আল জিহাদ বাংলাদেশ, ওয়ারত ইসলামিক ফ্রন্ট, জামায়াত-আস-সাদাত, আল খিদমত, হরকত-এ ইসলাম আল জিহাদ, হিজবুল্লাহ ইসলামী সমাজ, মুসলিম মিল্লাত শরিয়া কাউন্সিল, ওয়ার্ল্ড ইসলামিক ফ্রন্ট ফর জিহাদ, জইশে মুহাম্মদ, তা আমীর উদদ্বীন বাংলাদেশ, হিজবুল মাহাদী, আল ইসলাম মার্টারস বিগ্রেড ও তানজীম। এছাড়াও বাংলাদেশ। সরকার বিভিন্ন সময় নিষিদ্ধ করেছে চারটি আত্মস্বীকৃত ইসলামিক জঙ্গি সংগঠনকে; এগুলো হলো : শাহাদাত-ই-আল হিকমা (২০০৪) জমিয়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি, ২০০৫), জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি, ২০০৫)। এবং হরকাতুল জিহাদ (২০০৫) প্রভৃতি। বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের আমলে জমিয়াতুল মুজাহিদীন, জাগ্রত মুসলিম জনতা, শাহাদাত ই আল হিকমা এবং হরকাতুল জিহাদ (হুজি) কে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। নিষিদ্ধ তালিকায় সর্বশেষ সংযোজন হিযবুত তাহরি।
২৫৮ হাবিবুর রহমান, বাংলাদেশে জঙ্গি হামলার আশঙ্কা, বৃহস্পতিবার, ০৮ এপ্রিল ২০১০, নিউজ বাংলা।
২৫৯ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন The Clash of Fundamentalisms : Crusades, Jihads and Modernity, by Tariq Ali, Verso; Pbk edition (April, 2003); Rogue State: A Guide to the World’s Only Superpower by William Blum, Common Courage Press (May, 2000);ইত্যাদি।
২৬০ Ibn Ishaq, The Life of Muhammad, trs. A Guillaume, Oxford University Press, Karachi, 2004 imprint, p545
২৬১ Tabari, Abu Ja’far Muhammad b. Jarir, ‘The Victory of Islam’, vol viii, pp.35-36
২৬২ K. Armstrong Muhammad : A Western Attempt to Understand Islam, Gollanz, 1991, London, p. 207.
২৬৩ আকাশ মালিক, যে সত্য বলা হয়নি, মুক্তমনা ই-বুক। এম এ থান, জিহাদ : জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তরকরণ, সাম্রাজ্যবাদ ও দাসত্বের উত্তরাধিকার, বদ্বীপ প্রকাশন, ২০১০। Ali Sina, Understanding Muhammad: A Psychobiography of Allah’s prophet, Felibri.com, 2008. Ali Dashti, Twenty Three Years: A Study of the Prophetic Career of Mohammad, Mazda Pub; 1994 ইত্যাদি।
২৬৪ Noam Chomsky, 9-11, Open Media/Seven Stories Press; 2001
২৬৫ Fareed Zakaria, The Future of Freedom : Illiberal Democracy at Home and Abroad, W. W. Norton & Company; Revised Edition edition, 2007
২৬৬ Sam Harris, The End of Faith : Religion, Terror, and the Future of Reason, W. W. Norton, 2005
২৬৭ কোরআন শরীফ (বঙ্গানুবাদ) পূর্বোক্ত।
২৬৮ কোরআন শরীফ (বঙ্গানুবাদ) পূর্বোক্ত।
২৬৯ কোরআন শরীফ (বঙ্গানুবাদ) পূর্বোক্ত
২৭০ Terrorist and Insurgent Organizations, Air University Library Publications.
২৭১ সাদ কামালী এবং অভিজিৎ রায় (সম্পাদনা), স্বতন্ত্র ভাবনা, চারদিক, ২০০৮
২৭২ বাল্মীকি রামায়ণ, হেমচন্দ্র অনুদিত, রিফেকট পাবলিকেশন, কলিকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ১০৬৭-৭১
২৭৩ মহাকাব্যগুলোতে মনুর প্রভাব বিষয়ে আলোচনার জন্য দেখুন : মহাকাব্য ও মৌলবাদ, জয়ন্তানুজ বন্দ্যোপাধ্যায়, এলাইড পাবলিশার্স লিমিটেড, কলিকাতা। এবং Laws of Manu, translated with extracts from seven commentaries by G. Buhler, ed. F. Max Muller, Clarendon Press, Oxford, 1886.
২৭৪ সুকুমারী ভট্টাচার্য, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, দীপ প্রকাশন, ২০০০।
২৭৫ পবিত্র বাইবেল, পুরতন ও নূতন নিয়ম, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি, ঢাকা, ২০০০
২৭৬ The Dark Bible, Compiled by Jim Walker,
http://www.nobeliefs.com/DarkBible/DarkBibleContents.htm
২৭৭ পবিত্র বাইবেল,পূর্বোক্ত
২৭৮ পবিত্র বাইবেল, পূর্বোক্ত
২৭৯ ‘অবিশ্বাসের দর্শন’ বইটার প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পর মুসলিমদের মত কিছু হিন্দু মননকেও আহত করে ফেলেছিল। এক মডারেট হিন্দু বইটার রিভিউ করতে গিয়ে একটা ব্লগ সাইটে লিখে দিলেন– সতীদাহের পুরো ব্যাপারটাই নাকি সাংস্কৃতিক, ধর্মগ্রন্থে নাকি সতীদাহের কোন অস্তিত্ব নেই। আসলে এই ‘মডারেট’ হিন্দুরা নিজের ধর্মগ্রন্থটাও ঠিকমত পড়ে দেখেন না। এরা জানেন না তাদের ধর্মগ্রন্থে স্বামী মারা গেলে বিধবাকে স্বামীর চিতায় আগুনে পুড়ে মরে সতী হওয়ার সুস্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। যেমন, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৪নং সূক্তের ৭ নং ঋক (১০/১৪/৭) দ্রষ্টব্য :
इमा नारीररावधवाः सुपत्नीराजनैन सर्पिषा संविशन्तु
अनअ.अनमीवाः सुत्ना आ रोहन्तु जनयोयोनिम
: ‘Let these women, whose husbands are worthy and are living, enter the house with ghee (applied) as collyrium (to their eyes). Let these wives first step into the pyre, tearless without any affliction and well adorned.’
অথর্ববেদে রয়েছে : ‘আমরা মৃতের বধূ হবার জন্য জীবিত নারীকে নীত হতে দেখেছি। (১৪/৩/১,৩)। পরাশর সংহিতায় পাই, ‘মানুষের শরীরে সাড়ে তিন কোটি লোম থাকে, যে নারী মৃত্যুতেও তার স্বামীকে অনুগমন করে, সে স্বামীর সঙ্গে ৩৩ কোটি বৎসরই স্বর্গবাস করে (৪:২৪)। দক্ষ সংহিতার ৪:১৮-১৯নং শ্লোকে বলা হয়েছে, ‘যে সতী নারী স্বামীর মৃত্যুর পর অগ্নিতে প্রবেশ করে সে স্বর্গে পূজা পায়”। এই দক্ষ সংহিতার। পরবর্তী শ্লোকে (৫:১৬০) বলা হয়েছে, ‘যে নারী স্বামীর চিতায় আত্মোৎসর্গ করে সে তার পিতৃকুল, স্বামীকুল উভয়কেই পবিত্র করে।”
২৮০ সত্যি কথা বলতে কি[আমরা নতুন দিনের নাস্তিকেরা আসলে বিন-লাদেন, মুফতি হান্নান, বাংলা ভাই, মোল্লা ওমর, খোমেনি বা মৌলানা মান্নানের মতো লোকদের তেমন একটা দোষ দেই না; অন্তত তারা কথায় আর কাজে এক। আল্লাহ কোরআনে যেভাবে বলেছেন, ঠিক সেভাবেই কোরআনের আদর্শকে সামনে রেখে তারা কাজ করে চলেছেন। আমরা আসলে দোষ দেই ‘শিক্ষিত এবং মডারেট’ তকমাধারী ধার্মিকদের যারা কোরআনের মধ্যে সহিষ্ণুতা খুঁজে পান আর চারিদিকে এত অশান্তি দেখেও ইসলাম শান্তির ধর্ম বলতে বলতে চুপ হয়ে যান। ঠিক একই ব্যাপার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের জন্যও খাটে। যারা রামের শাসনামলে শূদ্র তাপস শম্বুক কিংবা রামপত্নী সীতার কি করুণ অবস্থা হয়েছিল তা না জেনেই ‘রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন, অথবা বেদ, গীতা, উপনিষদ, মনুসংহিতায় কী আছে তা না জেনেই হিন্দু ধর্মকে সহিষ্ণুতম ধর্ম হিসেবে আখ্যা দিয়ে বসেন, আর মারামারি, হানাহানি আর সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির জন্য দায়ী করেন কেবল গুটিকয় আদভানী আর লালু প্রসাদকে।
২৮১ Victor J. Stenger, God : The Failed Hypothesis : How Science Shows That God Does Not Exist, Prometheus Books, 2007
২৮২ Ann Coulter, Godless : The Church of Liberalism, Three Rivers Press, 2007
২৮৩ Bill O’Reilly, Culture Warrior, Broadway, 2007
২৮৪ Kimberly Blaker, The Fundamentals of Extremism : The Christian Right in America, New Boston Books, 2003
২৮৫ প্রবীর ঘোষ, অলৌকিক নয়,লৌকিক, তৃতীয় খন্ড, দে’জ পাবলিশিং, পৃ. ৩৯।
২৮৬ The results of the Christians vs atheists in prison investigation, By Rod Swift, http://holysmoke.org/icr-pri.htm
২৮৭ Phil Zuckerman,. ‘Atheism : Contemporary Rates and Patterns’, chapter in The Cambridge Companion to Atheism, ed. by Michael Martin, Cambridge University Press : Cambridge, UK, 2005.
২৮৮ Phil Zuckerman, Society without God : What the Least Religious Nations Can Tell Us About Contentment, NYU Press, 2010
২৮৯ Something Happy in the State of Denmark, Los Angeles Times, June 19, 2006.
২৯০ Michael Shermer, The Science of Good & Evil : Why People Cheat, Gossip, Care, Share, and Follow the Golden Rule, Holt Paperbacks, 2004
২৯১ সাম্প্রতিক সময়গুলোতে জীববিজ্ঞান, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং বিবর্তনীয় উৎসের সন্ধান করে বহু বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ এবং গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়
* Robert Axelrod, The Evolution of Cooperation, Basic Books, 1985
* Richard Alexander, The Biology of Moral Systems, Aldine Transaction, 1987
* Robert Wright, The Moral Animal : Why We Are, the Way We Are : The New Science of Evolutionary Psychology, Vintage, 1995
* Frans B. M. de Waal, Good Natured : The Origins of Right and Wrong in Humans and Other Animals, Harvard University Press, 1997
* Larry Arnhart, Darwinian Natural Right : The Biological Ethics of Human Nature, State University of New York Press, 1998
* Leonard D. Katz, Evolutionary Origins of Morality : Cross-Disciplinary Perspectives, Imprint Academic, 2000
* Donald M. Broom, The Evolution of Morality and Religion, Cambridge University Press, 2004 ইত্যাদি
২৯২ Richard Dawkins, The Selfish Gene. Oxford: Oxford University Press. 1976
২৯৩ অভিজিৎ রায়, বিবর্তনের দৃষ্টিতে নৈতিকতার উদ্ভব (১ম এবং ২য় পর্ব), অক্টোবর ২১, ২০১০, মুক্তমনা
২৯৪ নাফিসের ঘটনার পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ অভিজিৎ রায়ের বিশ্বাসের ভাইরাস (জাগৃতি, ২০১৪) বইয়ে।
২৯৫ 9-11, Noam Chomsky, Open Media/Seven Stories Press, 1 edition, October 2001
২৯৬ Bruce Lincoln, Holy Terrors : Thinking About Religion After September 11, University Of Chicago Press; 2 edition, 2006
২৯৭ Last words of a terrorist, Guardian UK,
http://www.guardian.co.uk/world/2001/sep/30/terrorism.september113
২৯৮ Is Religion Killing Us? : Violence in the Bible and the Quran, Jack Nelson Pallmeyer, Trinity Press International, 2003
২৯৯ The End of Faith : Religion, Terror, and the Future of Reason, Sam Harris, W. W. Norton, 2005
৩০০ Islamabad Tells of Plot by Lashkar, Islamabad : Wall Street Journal, Retrieved 2009-07-28.
৩০১ অভিজিৎ রায়, বিশ্বাসের ভাইরাস, ১৪ অগ্রহায়ণ ১৪১৫ (২৮ নভেম্বর, ২০০৪), মুক্তমনা
৩০২ Richard Dawkins, What Use is Religion?, Free Inquiry magazine, Volume 24, Number 5. বাংলা- ধর্মের উপযোগিতা, মুক্তমনা
৩০৩ Breaking the Spell : Religion as a Natural Phenomenon, Daniel C. Dennett, Viking Adult, 2006
৩০৪ Shaoni Bhattacharya, Parasites brainwash grasshoppers into death dive, New Scientists, August 2005
৩০৫ Darrel W. Ray, The God Virus : How religion infects our lives and culture, IPC Press; First edition, December 5, 2009
৩০৬ Bruce Lincoln, Holy Terrors : Thinking about Religion after September 11, University Of Chicago Press; 1 edition, 2003
৩০৭ Richard Dawkins, Design for a Faith-Based Missile, Volume 22, Number 1.
৩০৮ অভিজিৎ রায়, সমকামিতা : একটি বৈজ্ঞানিক এবং সমাজ মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধান, শুদ্ধস্বর, ২০১০, পৃ ১৭২-১৯৮
৩০৯ The Selfish Gene, Richard Dawkins, Oxford University Press, 1976
৩১০ বিজ্ঞান ও ধর্ম : সংঘাত নাকি সমন্বয়? ২০০৪, মুক্তমনা ই বুক,
http://www.mukto-mona.com/project/Biggan_dhormo2008/
৩১১ ‘বিজ্ঞান ও ধর্ম : সংঘাত নাকি সমন্বয’ বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়
৩১২ Richard Brodie, Virus of the Mind: The New Science of the Meme, Hay House, 2009; Craig A. James, The Religion Virus: Why We Believe in God: An Evolutionist Explains Religion’s Incredible Hold on Humanity, O Books, John Hunt, 2010
৩১৩ Nigel Davies, Human Sacrifice–In History and Today, William Morrow & Co; 1981
৩১৪ বেশকিছু উদাহরণ নেওয়া হয়েছে Holy Horrors : An Illustrated History of Religious Murder and Madness, James A. Haught, Prometheus Books, 1990 থেকে, সাম্প্রতিক কিছু উদাহরণ বিভিন্ন পত্রপত্রিকা এবং মুক্তমনা সাইট থেকে।
৩১৫ Alan S. Miller & Satoshi Kanazawa, Why Beautiful People Have More Daughters : From Dating, Shopping, and Praying to Going to War and Becoming a Billionaire– Two Evolutionary Psychologists Explain Why We Do What We Do, Perigee Trade, 2008
৩১৬ বিশ্বাসের ভাইরাস এবং আনুষঙ্গিক, দিগন্ত সরকার, মুক্তমনা,
http://mukto-mona.com/banga_blog/?p=325
৩১৭ In the Name of History Examples from Hindutva-inspired school textbooks in India, Online : http://www.sacw.net/HateEducation/Teesta.html
৩১৮ Satoshi Kanazawa, Why Liberals And Atheists Are More Intelligent.
৩১৯ Satoshi Kanazawa, Why Liberals Are More Intelligent Than Conservatives, Psychology Today, March 21, 2010
৩২০ Satoshi Kanazawa, Why Atheists Are More Intelligent than the Religious, Psychology Today, April 11, 2010
৩২১ Jaime E. Settle, Christopher T. Dawes, Nicholas A. Christakis, James H. Fowler. Friendships Moderate an Association between a Dopamine Gene Variant and Political Ideology. The Journal of Politics, 2010; 72 (04): 1189
৩২২ Religiosity Highest in World’s Poorest Nations, Gallup’s global reports, August 31, 2010
৩২৩ Charles M. Blow, Religious Outlier, The Newyork Times, Published : September 3, 2010
৩২৪ World Publics Welcome Global Trade— But Not Immigration, Summary of Findings, http://pewglobal.org/2007/10/04/world-publics-welcome global-trade-but-not-immigration/
৩২৫ মুম্বাই এ ফিদাইন হানা- একটি বিশ্লেষণ, বিপ্লব পাল, মুক্তমনা
online : http://mukto-mona.com/banga_blog/?p=288
৩২৬ অভিজিৎ রায়, বিশ্বাসের ভাইরাস, জাগৃতি, ২০১৪
৩২৭ Darrel W. Ray, The God Virus : How religion infects our lives and culture, IPC Press; First edition, December 5, 2009
৩২৮ পবিত্র বাইবেলে আছে,
‘আর জগৎও অটলতা বিচলিত হবে না’ (ক্রনিকলস ১৬/৩০)।
‘জগৎ ও সুস্থির, তা নড়াচড়া করবে না।’ (সাম ৯৩/১)
‘তিনি পৃথিবীকে অনড় এবং অচল করেছেন’ (সাম ৯৬/১০)
‘তিনি পৃথিবীকে এর ভিত্তিমূলের ওপর স্থাপন করেছেন, তা কখনো। বিচলিত হবে না’ (সাম ১০৪/৫) ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে আরও দেখুন বইয়ের ষষ্ঠ (বিজ্ঞানময় কিতাব) অধ্যায়টি।
৩২৯ অভিজিৎ রায়, আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৬
৩৩০ এ প্রসঙ্গে দেখুন, নুরুজ্জামান মানিক, ইসলামের চিন্তার ইতিহাসে যারা সত্যের শহীদ, ‘বিজ্ঞান ও ধর্ম- সংঘাত নাকি সমন্বয়?”, মুক্তমনা ই-বুক।
৩৩১ রিচার্ড ডকিন্স তাঁর গড ডিলুশন’ বইয়ে কার্গো কাল্টদের নিয়ে আলাদা ভাবে লিখেছেন Richard Dawkins, God Delusion, Houghton Mifflin Harcourt; 1st Am. ed. Edition, 2006 PP. 202-207.
৩৩২ মূল প্রতিবেদনের স্ক্যানড কপি রাখা আছে,
http://www.somewhereinblog.net/blog/omipialblog/28734445
৩৩৩ Adolf Hitler, Mein Kampf, Houghton Mifflin, New York : Hutchinson Publ. Ltd., London, 1969, p 60.
৩৩৪ Adolf Hitler, in a speech on 12 April 1922 (From Norman H. Baynes, ed. The Speeches of Adolf Hitler, April 1922-August 1939, Vol. 1 of 2, pp. 19 20, Oxford University Press, 1942)
৩৩৫ www.nobeliefs.com/hitler.htm–এই সাইটে হিটলারের খ্রিস্টিয় বিশ্বাস এবং অনুপ্রেরণা নিয়ে বেশ কিছু ভাল আলোচনা রয়েছে।
৩৩৬ যেমন, আইওয়া স্টেট রিলিজিয়াস স্টাডিজ-এর অধ্যাপক হেকটর এভালজ তাঁর Fighting Words : The Origins Of Religious Violence US গ্রন্থে খুব পরিষ্কারভাবেই দেখাতে সমর্থ হয়েছেন যে, কোথাওই নাস্তিকতার জন্য স্ট্যালিন গণহত্যা করেন নি, করেছেন তার কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাসপ্রসূত রাজনীতির (collectivization) কারণে।
৩৩৭ Edvard Radzinsky, Stalin : The First In-depth Biography Based on Explosive New Documents from Russia’s Secret Archives, Anchor, 1997
৩৩৮ এ প্রসঙ্গে পড়ুন–এই বইয়ের পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ নাস্তিকতাও একটি ধর্ম (বিশ্বাস) হলে…
৩৩৯ আমেরিকার ফাউন্ডিং ফাদারদের প্রধান ছিলেন যারা তাদের অনেকেই আসলে ধর্মহীন নাস্তিক ছিলেন বলে অনেকে দাবি করেন। ক্রিস্টোফার হিচেন্স তাঁর ‘Thomas Jefferson : Author of America’ বইয়ে দাবি করেছেন যে, জেফারসন সম্ভবত নাস্তিকই ছিলেন, এমনকি তার সময়েও এবং প্রবলভাবেই। রিচার্ড ডকিন্সও তাঁর God Delusion বইয়ে এমন ইঙ্গিত করেছেন। তবে নাস্তিক হোন বা না হোন আমেরিকার ফাউন্ডিং ফাদারেরা যে সেকুলার ছিলেন, এটা তাদের বিভিন্ন লেখালেখি থেকে স্পষ্ট। পরবর্তীকালে ফাউন্ডিং ফাদারদের আদর্শ থেকে আমেরিকার বিচ্যুতি প্রবলভাবে লক্ষণীয়। আমেরিকার ডলারে লিখিত ‘ইন গড উই ট্রাস্ট’ এমন একটি উদাহরণ।
৩৪০ বইয়ের সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
৩৪১ Keith Ward, In Defence of The Soul, Oneworld Publications, May 25, 1998
৩৪২ John Caputo, On Religion (Thinking in Action), Routledge, 2001
৩৪৩ বইয়ের সপ্তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।
৩৪৪ Eric Kaufmann, ‘Sacralization by Stealth : Religion Returns to Europe’, Riley Institute Public Lecture, Furman University, Greenville, SC.
৩৪৫ জাহানারা ইমাম স্মারক সভায় ড. অজয় রায়ের বক্তৃতা
http://www.mukto mona.com/award/award_ajoy_unic.htm
৩৪৬ http://www.mukto-mona.com/human-rights/report.htm
৩৪৭ অজয় রায়, আমার বন্ধু নির্মল সেন : স্বস্তিতে নেই (সাহায্যের আবেদনপে প্যাল আপডেট)– নির্মল সেনের সাহায্যের এই আবেদনটি মুক্তমনায় প্রচারিত হওয়ার পরে অনেক সহৃদয় ব্যক্তি সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছেন। ফলে আমরা খুব কম সময়ের মধ্যেই আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য ১০০০ ডলার তোলার লক্ষ্য পূরণে সফল হয়েছিলাম।
৩৪৮ ‘আদিল মাহমুদ, একটি মানবিক আবেদন[একজন মা’–আমরা মুক্তমনার পক্ষ থেকে প্রায় বারো দিন ব্যাপী ফান্ড রেইজিং শেষে আরিফের মায়ের চিকিৎসার জন্য ১৭২৫.০৩ $ USD সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলাম।
৩৪৯ The American Religious Identification Survey gave Non-Religious groups the largest gain in terms of absolute numbers- 14,300,000 (8.4% of the population) to 29,400,000 (14.1% of the population) for the period 1990 to 2001 in the USA.
Also, in Australia, census data from the Australian Bureau of Statistics gives ‘no religion’ the largest gains in absolute numbers over the 15 years from 1991 to 2006, from 2,948,888 (18.2% of the population that answered the question) to 3,706,555 (21.0% of the population that answered the question).
৩৫০ Darwin’s Dangerous Idea : Conflict Between God & Theory of Evolution, MM Collection, ://www.mukto mona.com/Special_Event_/Darwin_day/god_darwin/index.htm
৩৫১ আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী, অভিজিৎ রায়, অঙ্কুর প্রকাশনী (২০০৫, পুনঃমুদ্রণ ২০০৬)।
৩৫২ www.mukto-mona.com এবং www.infidels.org ওয়েবসাইট দুটি দেখতে পারেন।
৩৫৩ আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী (অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০৫)
৩৫৪ মূল বইয়ের সপ্তম অধ্যায় দেখুন।
৩৫৫ E.P. Tryon, ‘Is the Universe a Vacuum Fluctuation?’, Nature 246 (1973): 396-97.
৩৫৬ বিস্তারিত তথ্যের জন্য The Inflationary Universe : The Quest for a New Theory of Cosmic Origins, Alan H. Guth, Perseus Books Group (March 1, 1998) দেখুন।
৩৫৭ মীজান রহমান এবং অভিজিৎ রায়, শূন্য থেকে মহাবিশ্ব, শুদ্ধস্বর, ২০১৫ (প্রকাশিতব্য)।
৩৫৮ Self Reproducing Inflationary Universe, Andrei Linde, Scientific American, 1998
৩৫৯ অনন্ত মহাবিশ্বের সন্ধানে, অভিজিৎ রায়, দৈনিক সমকাল, ১৫ জুলাই ২০০৬
৩৬০ Endless Universe : Beyond the Big Bang– Rewriting Cosmic History by Paul J. Steinhardt and Neil, Broadway; Reprint edition (June 3, 2008)
.
যাদের কাছে ঋণী
প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে ব্যবহৃত মনীষীদের বেশ কয়েকটি উদ্ধৃতি সংগ্রহ এবং অনুবাদ করেছেন ধর্মকারী ওযেবসাইটের (www.dhormockery.com) সঞ্চালক। বিজ্ঞান লেখক বন্যা আহমেদ এ বইয়ের বিবর্তন অংশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পাঠ করে মতামত দিয়েছেন। পদার্থবিজ্ঞান অংশে কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানী তানভীরুল ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ অভিমত আকণ্ঠ ঋণী করেছে আমাদের। বইয়ের অংশবিশেষ মুক্তমনা এবং ক্যাডেট কলেজ ব্লগে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশের সময় বহু পাঠক তাদের সুচিন্তিত মতামত দিয়েছিলেন। সেই মতামত এবং পরামর্শগুলো গ্রন্থের মানোন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। ঋণী আমরা তাদের কাছেও। ‘ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো’র মন্ত্রে উজ্জীবিত বাংলা ব্লগগুলোর মুক্তমনা লেখকরা, যারা ধর্ম এবং ঈশ্বর-সংক্রান্ত প্রান্তিক প্রশ্নগুলো নিয়ে সাহসী লেখা লিখে চলছেন নিয়মিত, কখনো সেসব করতে গিয়ে হয়েছেন মৌলবাদীদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু কিংবা রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের শিকার, তাদের প্রতিও রইলো কৃতজ্ঞতা। চমৎকার এবং চিন্তা-জাগানিয়া একটি প্রচ্ছদ করে আমাদের অভিভূত করে দিয়েছেন সামিয়া হোসেন।
শুদ্ধস্বরের প্রকাশক আহমেদুর রশীদ টুটুল বইটির প্রথম দুটো সংস্করণ প্রকাশ করে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। কিন্তু পাশাপাশি পাঠক মহলে বিশাল চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বইটিকে দীর্ঘদিন ‘আউট অফ প্রিন্ট’ হিসেবে রেখে দেওয়ায় আমাদেরকে বেদনার্তও করেছেন। পুরোমাত্রায়। এই ক্রান্তি লগ্নে বইটির গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করে জাগৃতি প্রকাশনীর তরুণ প্রকাশক ফয়সল আরেফিন দীপন বইটির সমস্ত ভার নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বইটি অতি দ্রুত প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। এ কৃতিত্বটুকু তরুণ, উদ্যমী এবং সাহসী এ প্রকাশকের অবশ্যই প্রাপ্য। আমাদের যুক্তিবাদী আন্দোলনের পরিচিত মুখ এবং যুক্তি পত্রিকার সম্পাদক অনন্ত বিজয় দাশ সময় নিয়ে বইটির প্রথম সংস্করণের প্রুফ রিডিং করেছিলেন। স্বল্প সময়ের মাঝে প্রথম সংস্করণের কাজ শেষ করায় বইটিতে থেকে গিযেছিল বেশ কিছু অনিচ্ছাকত ত্রুটি। সে সময় বেশ কিছু বানানপ্রমাদ চিহ্নিত করেছিলেন শাহরিয়ার মামুন রনি। তবে একটি পরিমার্জিত এবং সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ সে সময় এসেছিল তরুণ লেখক এবং গবেষক অঞ্জন আচার্যের বদান্যতায়। আর, বইটির শেষ সংস্করণ প্রকাশের পর বইটি নিয়ে ব্লগে এবং ম্যাগাজিনে দুটো চমৎকার গ্রন্থ পর্যালোচনা করেছেন ব্লগার শফিউল জয় এবং ড. প্রদীপ দেব। পাশাপাশি কিছু ত্রুটি বিচ্যুতিরও উল্লেখ করেছিলেন তারা। অজানা অচেনা অনেক পাঠকদের কাছ থেকেও টুকিটাকি কিছু সংশোধনী এসেছে। আমরা আনন্দিত যে, সে সব ভুল ত্রুটি সংশোধন করে তৃতীয় সংস্করণ অবশেষে আলোর মুখ দেখছে। বইটির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যারা জড়িত ছিলেন সবার প্রতি রইলো আমাদের কৃতজ্ঞতা।