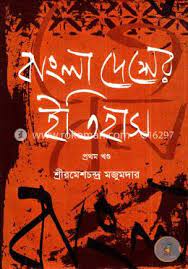- বইয়ের নামঃ বাংলা দেশের ইতিহাস – ১ম খণ্ড
- লেখকের নামঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার
- প্রকাশনাঃ দিব্য প্রকাশ
- বিভাগসমূহঃ ইতিহাস
০. প্রসঙ্গকথা / ভূমিকা
প্রথম খণ্ড (প্রাচীন যুগ) –শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার
উৎসর্গপত্র
অতি শৈশবেই যাহার ক্রোড়চ্যুত হইয়াছিলাম সেই পরমারাধ্যা পুণ্যফলে স্বর্গগতা জননী বিধুমুখী দেবী ও মাতৃহীন হইয়াও যাহার করুণায় মাতৃস্নেহ হইতে বঞ্চিত হই নাই সেই পুত-চরিত্রা স্বর্গীয়া মাতৃকল্পা গঙ্গামণি দেবীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে জন্মভূমির এই ক্ষুদ্র ইতিহাস উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইলাম।
জননী ও জন্মভূমি স্বর্গ হইতেও শ্রেষ্ঠ
.
প্রসঙ্গকথা (বর্ত্তমান সংস্করণ)
প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস লেখার পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। এর বড় কারণ সমকালে লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায়নি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় রাজ পৃষ্ঠপোষকতায় দরবারী ইতিহাসও লেখা হয়নি। ফলে সাহিত্যের সূত্র, পর্যটকদের বিবরণ এবং সামান্য প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ব্যবহার করে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস লেখা আধুনিক কালের একটি প্রয়াস বলা যেতে পারে। মধ্যযুগের ইতিহাস লেখায় বাড়তি সুযোগ এসেছে দিল্লিতে বসে সুলতান ও মোগল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় লেখা দরবারী ইতিহাস। এসব সূত্র ব্যবহার করে লেখা ইতিহাস রাজনৈতিক ইতিহাসের গণ্ডি পেরুতে পারেনি অনেক কাল পর্য্যন্ত। সেই অর্থে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস লেখা একেবারে সাম্প্রতিক কালের প্রয়াস। এমন বাস্তবতার আদি সময়ে অনেকটা শূন্যতার মধ্য দিয়েই রমেশচন্দ্র মজুমদারকে বাংলা দেশের ইতিহাস নামে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস লেখার যাত্রা শুরু করতে হয়েছিল। গত শতকের চল্লিশের দশকে রমেশ চন্দ্র মজুমদার যখন বাংলা ভাষায় বাংলার ইতিহাস লেখার পরিকল্পনা করেন তার অনেক বছর আগে অনেকটা বিজ্ঞানসম্মতভাবে লেখা দুটো মাত্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এর একটি গৌড়রাজমালা। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ববিদ রাম প্রসাদ চন্দের এই বইটি বাংলা ১৩৩৯ সাল অর্থাৎ ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এটি পূর্ণাঙ্গ কোনো বাংলার ইতিহাস নয়। তবু বাংলার ইতিহাস রচনার পথে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ বলা যায়। এর দুই বছর পর বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ভাষায় রচনা করেন বাঙ্গালার ইতিহাস। এরপর দীর্ঘ বিরতি কাটিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দুই খণ্ডে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার ইতিহাস লেখার প্রকল্প গ্রহণ করে। সিদ্ধান্ত হয় গ্রন্থ দুটো হবে ইতিহাসবিদ ও গবেষকদের প্রবন্ধের সংকলন। প্রাচীন যুগের গ্রন্থটি রমেশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় (R.C. Majumdar) The History of Bengal Volume-1, Hindu Period) নামে ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। রমেশচন্দ্র মজুমদার আশা করেছিলেন গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেই উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। ব্যক্তিগত আগ্রহে ও দায়বোধ থেকে শেষ পর্য্যন্ত তিনি প্রাচীন যুগপর্বের বাংলাদেশের ইতিহাস লেখায় আত্মনিয়োগ করেন।
এই গ্রন্থ রচনায় রমেশচন্দ্র মজুমদার একজন মেধাবি ঐতিহাসিকের স্বাক্ষর রাখতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় নিজেই উল্লেখ করেছেন এই গ্রন্থ তিনি টিকা টিপ্পনির ভারে ভারাক্রান্ত করতে চাননি। সহজবোধ্যভাবে যেন পাঠক আত্মস্থ করতে পারে। অথচ তারপরেও নানা তথ্যে সমৃদ্ধ একটি অভিজাত ইতিহাস গ্রন্থই তিনি উপস্থাপন করেছিলেন।
আমরা দেখেছি বিশ শতক পর্য্যন্ত কালপরিসরের মধ্যে অল্প কয়েকজন ইতিহাসবিদের প্রয়াস ছাড়া প্রায় সকল ইতিহাস গ্রন্থই রাজনৈতিক ইতিহাসে আটকে ছিল। সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস চর্চ্চা তেমনভাবে অগ্রসর হয়নি। এর বড় কারণ সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস লেখার মত তথ্য সূত্রের অভাব। সাম্প্রতিক সময়ে প্রত্নসূত্র অনুসন্ধানের সুযোগ তৈরি হওয়ায় নতুন করে বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস লেখার ধারা শুরু হয়েছে।
অথচ রমেশচন্দ্র মজুমদারের ব্যক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতা সূত্র সংকটের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে সাহায্য করেছে। তাই তাঁর গ্রন্থে (বাংলাদেশের ইতিহাস) অত্যন্ত সার্থকভাবে রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের একটি ধারাবাহিকতা উপস্থাপিত হয়েছে অনেকটা স্পষ্টভাবেই।
ইতিহাসে একটি কথা রয়েছে যে ইতিহাস বা ইতিহাসের ঘটনা বার বার ফিরে আসে। এজন্যই হয়তো বলা হয় ইতিহাসে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া যায় না। শেষ সত্যে পৌঁছা যায় না, তবে নতুন নতুন তথ্যে বার বার সংস্কার করে সত্যের দিকে এগিয়ে চলা যায়। রমেশচন্দ্র মজুমদার যে সময়ে বাংলাদেশের ইতিহাস রচনা করেছিলেন তখন প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্র প্রাপ্তির সীমাবদ্ধতা থাকলেও নিজ মেধা প্রয়োগ করে তিনি অনেক বাধাই অতিক্রম করতে পেরেছিলেন।
একারণেই তাঁর গ্রন্থে রাজনৈতিক ইতিহাসের পাশাপাশি প্রাচীন বাংলার সমাজ, ধর্ম্ম, শিল্পকলা সকল কিছুই অত্যন্ত গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। রমেশচন্দ্র মজুমদার ছিলেন একজন বিদগ্ধ ইতিহাসবিদ। একজন ইতিহাস পাঠককে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস জানানোর জন্য যেভাবে সূচি বিন্যাস করা দরকার তিনি এই গ্রন্থে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তা করতে পেরেছেন। ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থান বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে পাঠককে পরিচিত করিয়েছেন বাংলাদেশের সাথে। নৃতাত্ত্বিক নানা বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে চিহ্নিত করা হয়েছে এই গ্রন্থে। এই জাতির উৎপত্তি ও বিকাশ ধারা উন্মোচিত হয়েছে। রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারাক্রম আলোচনায় অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে শাসকদের শাসনকালের বর্ণনা করেছেন গ্রন্থকার।
আমরা বলতেই পারি প্রাচীন বাংলার ইতিহাস রচনায় সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাস বিশেষ করে শিল্প ইতিহাস রচনার পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন রমেশচন্দ্র মজুমদার তার গ্রন্থের শেষ পর্বে।
অবশ্য বাংলা দেশের ইতিহাস পাঠ করা সমালোচকদের অভিযোগ রয়েছে রমেশচন্দ্র মজুমদারের মধ্যে কিছুটা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করেছে। কারণ তিনি হিন্দুদের পাশাপাশি সাধারণ মুসলমানদের কথা বলতে গিয়ে প্রায়ই ম্লেচ্ছ ও যবন বলে অভিহিত করেছেন তাঁর গ্রন্থে। কোনো কোনো জায়গায় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ বিশ্লেষণে কিছুটা একদেশদর্শিতার সংকট রয়েছে। অবশ্য বঙ্গভঙ্গোত্তর বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিরোধের দেয়াল তৈরি করা হয়েছিল তাতে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির মুসলমান ও একই ধারার হিন্দু অবস্থান পুরুষানুক্রমে টিকে ছিল। আর. সি. মজুমদারের ইতিহাস চর্চ্চা কখনো কখনো খুব সীমিতভাবে হলেও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাকে এড়াতে পারেনি। পাঠক যদি সময়ের বাস্তবতা মেনে পাঠ করেন তবে খুব একটা অস্বস্তিতে পরতে হবে না।
এ কথাটি ঠিক রমেশচন্দ্র মজুমদার যখন গবেষণা করেন তখন প্রত্নউপাদানের অনেকটাই আবিষ্কৃত হয়নি। তাই কোনো কোনো ঘটনা বা সন তারিখ সচেতন মানুষের কাছে ভুল মনে হতে পারে। যেমন তিনি বখতিয়ার খলজির নদীয়া আক্রমণের তারিখ ১২০২ বলেছিলেন। এই তারিখ নিয়ে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত গবেষকদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছিল। প্রায় আড়াই দশক আগে আমরা বখতিয়ার খলজির মুদ্রা শনাক্ত করতে পারি। আর মুদ্রা উত্তীর্ণের তারিখ যাচাই করে বলতে পারি নদীয়া আক্রমণের তারিখটি ছিল ১২০৪। ইতিহাস লিখনের এটিই রীতি। এভাবেই যুগে যুগে সংশোধিত হয় প্রাপ্ত নতুন উপাদান ব্যবহার করে। তাই ‘বাংলা দেশের ইতিহাস’ গ্রন্থে এজাতীয় তথ্য ভুল না ভেবে নির্দিষ্ট সময়ের সিদ্ধান্ত বলে মানতে হবে।
পাশাপাশি বখতিয়ার খলজি (ইখতিয়ার উদ্দিন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি) প্রসঙ্গে বর্ত্তমান গ্রন্থটিতে আরেকটি বিশ্লেষণ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মত প্রকৃত ইতিহাসবিদের দৃষ্টিভঙ্গিকে স্পষ্ট করছে। ইতিহাসের একটি ভুল ব্যাখ্যা দীর্ঘদিন থেকে আমরা বহন করে আসছিলাম। আর তা হচ্ছে ‘বখতিয়ারের বঙ্গ বিজয়’। ১৯৯৬-এ এনসিটিবির পাঠ্য বই, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বই ইত্যাদিতে সংস্কার করে আমরা লিখছি বখতিয়ারের অধিকৃত অঞ্চল ‘বঙ্গ’ নয় নদীয়া ও লখনৌতি। অর্থাৎ প্রাচীন জনপদ বঙ্গের সীমানায় বখতিয়ার প্রবেশ করেননি। আবার বখতিয়ারের অনেক পরে মানচিত্রে বাংলা বা বাংলাদেশ নামে একটি ভূখণ্ড চিহ্নিত হয়েছে। বিশেষ করে ১৩৫২-৫৩ খ্রিস্টাব্দে সুলতান শামস উদ্দিন ইলিয়াস শাহ পুরো বাংলাকে একটি সার্বভৌম দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পর। সুতরাং বখতিয়ার প্রকৃত অর্থে বাংলা বা বঙ্গ বিজেতা নন। বাংলায় মুসলিম বিজয়ের দ্বারোঘাটন করেছিলেন মাত্র। অথচ অত আগে প্রত্নসূত্র না থাকলেও নিজ প্রজ্ঞা দিয়ে রমেশচন্দ্র মজুমদার একটি যৌক্তিক ব্যাখ্যায় ইতিহাসের সত্যটিই উপস্থিত করেছিলেন অত্যন্ত সার্থকভাবে। বর্ত্তমান গ্রন্থের পাঠক মাত্রই ড. মজুমদারের অমন পাণ্ডিত্যের ছোঁয়ায় মুগ্ধ হবেন।
মুদ্রণ না থাকায় এই অসাধারণ গ্রন্থটি দীর্ঘকাল সহজলভ্য ছিল না। দিব্যপ্রকাশ ধ্রুপদী ইতিহাস গ্রন্থ পুণঃমুদ্রণ করে, অনুবাদ করিয়ে প্রকাশ করায় একটি প্রতীকী প্রতিষ্ঠান হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে। রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাংলা দেশের ইতিহাস গ্রন্থটি প্রকাশ করে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করলো। দিব্যপ্রকাশের কর্ণধার প্রীতিভাজন সুলেখক মঈনুল আহসান সাবের যখন প্রকাশের পূর্ব্বে এই বইখানির একটি ভূমিকা লিখে দিতে বললেন, তখন আমি বিব্রতবোধ করছিলাম। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মত ঐতিহাসিকের গ্রন্থের ভূমিকা লেখা আমার মত অর্ব্বাচীনের সাজে না। কিন্তু সাবের ভাইয়ের অনুরোধ ফেলা মুশকিল। তাই ভূমিকা নয়–গ্রন্থ প্রসঙ্গে দুএকটি কথা বলার সুযোগটুকু নিলাম।
ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ
অধ্যাপক
প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
.
প্রথম সংস্কর
প্রাচীন ভারতবাসিগণ সাহিত্যের নানা বিভাগে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, কিন্তু নিজেদের দেশের অতীত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার জন্য তাঁহাদের কোনো আগ্রহ বা উৎসাহ ছিল না। পণ্ডিতপ্রবর কহলণ রাজতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থে কাশ্মীরের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই শ্রেণীর আর কোনো গ্রন্থ অদ্যাবধি ভারতবর্ষে আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহার ফলে ভারতের প্রাচীন যুগের ইতিহাস একরকম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ ভারতের প্রাচীন লিপি, মুদ্রা ও অন্যান্য ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়া হিন্দু যুগের ইতিহাস উদ্ধারের সূচনা করেন। কালক্রমে অনেক ভারতবাসীও তাঁহাদের প্রবর্তিত পথে অনুসন্ধান-কার্যে অগ্রসর হইয়াছেন। ইহাদের সমবেত চেষ্টার ফলে যে সমুদয় তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে প্রাচীন যুগের ইতিহাসের কাঠামো রচনা করা সম্ভবপর হইয়াছে।
বাংলা দেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা যে কতদূর গভীর ছিল, ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যাপক পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় শর্মা রচিত রাজতরঙ্গ’ অথবা রাজাবলী’ গ্রন্থই তাঁহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বাংলার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বাঙ্গালী জাতির স্মৃতি ও জনশ্রুতি যে কতদূর বিকৃত হইয়াছিল, এবং পাঁচ-ছয় শত বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী জাতির ঐতিহাসিক সূত্র কিরূপে সমূলে ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল, এই গ্রন্থখানি পড়িলেই তাহা বেশ বোঝা যায়।
পরবর্ত্তী একশত বৎসরে পুরাতত্ত্ব আলোচনার ফলে বাংলার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল, স্বর্গীয় রামপ্রসাদ চন্দ প্রণীত ‘গৌড়রাজমালা’ গ্রন্থখানি তাঁহার প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে। এদেশের অনেকে বিশেষত প্রাচীণপন্থিগণ পুরাতত্ত্বকে ‘পাথুরে প্রমাণ’ বলিয়া উপহাস অথবা অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাচীন ইতিহাসের উদ্ধারে ইহার মূল্য যে কত বেশী, ‘রাজাবলী’র সহিত ‘গৌড়রাজমালা’র তুলনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।
‘গৌড়রাজমালা’ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে লিখিত বাংলার প্রথম ইতিহাস। ১৩৩৯ সনে ইহা প্রকাশিত হয়। ইহার দুই বৎসর পরে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাণীত ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’ প্রকাশিত হয়। নামে ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’ হইলেও, ইহা প্রকৃতপক্ষে বাংলা ও মগধের ইতিহাস।
উল্লিখিত দুইখানি গ্রন্থেই কেবলমাত্র রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। বাংলার একখানি পূর্ণাঙ্গ লিখিবার কল্পনা অনেকবার হইয়াছে। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে বাংলার গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল ইহার সূত্রপাত করেন, এবং পরবর্ত্তী ত্রিশ বৎসরে আরও দুই-একজন এইরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা ফলবতী হয় নাই। স্বর্গীয় দীনশেচন্দ্র সেন এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ‘বৃহৎ বঙ্গ’ নামে দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ একখানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন (১৩৪১ সন)। কিন্তু, অনেক মূল্যবান তথ্য থাকিলেও এই গ্রন্থ বাংলার ঐতিহাসিক বিবরণ হিসাবে বিদ্বজ্জনের নিকট সমাদর লাভ করে নাই।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতেই সর্বপ্রথমে বাংলার একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস প্রকাশিত হয়। আমার সম্পাদনায় তিন বৎসর হইল ইহার প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে। ইহাতে হিন্দু যুগের শেষ পর্য্যন্ত বাংলার ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ইংরেজিতে লিখিত। যখন ইহার প্রথম পরিকল্পনা হয়, তখন আমার ইচ্ছা ছিল যে, ইংরেজী গ্রন্থ বাহির হইবার পরই ইহার একখানি বাংলা অনুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু এই গ্রন্থ রচনায় বহু বিলম্ব হওয়ার ফলে, ইহার প্রকাশের পূর্ব্বেই আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে অবসর গ্রহণ করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান কর্তৃপক্ষগণ যে সত্বর ইহার বঙ্গানুবাদের কোনো ব্যবস্থা করিবেন, তাঁহার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। সুতরাং বাংলা ভাষায় বাংলার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস এবং বাঙ্গালীর ধৰ্ম্ম, শিল্প ও জীবনযাত্রার অন্যান্য বিভাগের মোটামুটি বিবরণসংবলিত একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন অনুভব করিয়া এই ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত বাংলার ইতিহাস যে এই গ্রন্থের আদর্শ ও প্রধান উপাদান, তাহা বলাই বাহুল্য।
এই গ্রন্থ সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের জন্য, সুতরাং ইহাতে যুক্তি-তর্ক দ্বারা ভিন্ন ভিন্নমতের নিরাস ও প্রমাণপঞ্জীযুক্ত পাদটীকা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়াছি। যাহারা এই সমুদয় জানিতে চাহেন, তাঁহারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ইংরেজী গ্রন্থখানি পাঠ করিতে পারেন। ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞ পাঠকের পক্ষে এই সমুদয় অনাবশ্যক, কারণ এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ ও গ্রন্থগুলি প্রায় সবই ইংরেজী ভাষায় লিখিত।
হিন্দু যুগের বাংলা দেশ সম্বন্ধে যে সমুদয় তথ্য এ যাবৎ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাঁহারই সারমর্ম সংক্ষিপ্ত আকারে বাঙ্গালী পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতেছি। যাঁহারা ইংরেজী ইতিহাসখানি পাঠ করিয়াছেন বা করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ অনাবশ্যক। কিন্তু যাঁহাদের ঐ গ্রন্থ পাঠের সুযোগ, সুবিধা অথবা সময় নাই, তাঁহারা ইহা পাঠ করিলে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করিতে পারিবেন। অবশ্য এই ইতিহাসের অতি সামান্যই আমরা জানি। কিন্তু এই গ্রন্থপাঠে যদি বাঙ্গালীর মনে দেশের প্রাচীন গৌরব সম্বন্ধে ক্ষীণ ধারণাও জন্মে এবং বাঙ্গালী জাতির অতীত ইতিহাস জানিবার জন্য কৌতূহল ও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার
৪নং বিপিন পাল রোড, কলিকাতা পৌষ, ১৩৫২
.
দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা
অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়াছে। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, বাঙ্গালীর মনে অতীত ইতিহাস জানিবার আগ্রহ জন্মিয়াছে। সাত শত বৎসর পরে বাঙ্গালী হিন্দু পরাধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়াছে। সুতরাং যে যুগের ইতিহাস এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা জানিবার আগ্রহ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইবে, এরূপ ভরসা করা যায়। এই জন্যই যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি করিয়া এই নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হইল।
এই সংস্করণে গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পরিশোধিত করা হইয়াছে। প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হইবার পর বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে যে সমুদয় নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ হরিকেল ও চন্দ্রদ্বীপের অবস্থান, রাত উপাধিধারী নতুন এক রাজবংশ, ভবদের ভট্টের বালবলভীভুজঙ্গ উপাধির অর্থ, বল্লালসেনের গ্রন্থালয় এবং তাঁহার রচিত নূতন একখানি গ্রন্থ, ময়নামতী পাহাড়ে আবিষ্কৃত ভাস্কর্যের নিদর্শন, নূতন বাঙ্গালী বৈদ্যক গ্রন্থাকার প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ২৫ খানি নূতন ছবিও যোগ করা হইয়াছে।
তিন বৎসর পূর্ব্বে যখন এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন গ্রন্থারম্ভে বাংলা দেশের নাম ও সীমা সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলাম, “পরিবর্ত্তনশীল রাজনৈতিক বিভাগের উপর নির্ভর করিয়া কোনো প্রদেশের সীমা ও সংজ্ঞা নির্ণয় করা যুক্তিযুক্ত নহে।” এই নীতির অনুসরণ করিয়া বঙ্গ-বিভাগ সত্ত্বেও এই ইতিহাসে বাংলা দেশের নাম ও সীমা সম্বন্ধে কোনো পরিবর্ত্তন করি নাই। যেখানে কোনো জিলা বা বিভাগের উল্লেখ আছে, সেখানেও অবিভক্ত বঙ্গে ইহা যেরূপ ছিল তাহাই বুঝিতে হইবে।
কিরূপে সুদূর প্রাচীনকাল, হইতে নানাবিধ বিবর্ত্তন ও পরিবর্ত্তনের ফলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীরা এক জাতিতে পরিণত হইয়াছিল, গ্রন্থশেষে তাঁহার আলোচনা করিয়াছি। বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সত্ত্বেও এই অংশের কোনো পরিবর্ত্তন করি নাই। কারণ অতীতকালের বাঙ্গালী যে এক জাতি ছিল, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। ভবিষ্যতের গর্ভে কী নিহিত আছে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। যদি বর্ত্তমান বিভাগ চিরস্থায়ী হইয়া দুই বাংলার অধিবাসীর মধ্যে আচার, কৃষ্টি ও ভাষাগত গুরুতর প্রভেদেরও সৃষ্টি হয়, তথাপি বাঙ্গালীর এক জাতীয়তার ঐতিহ্য চিরদিনই বাঙ্গালীর স্মৃতির ভাণ্ডারে সমুজ্জ্বল থাকিবে। হয়তো অতীতেও এই স্মৃতি ভবিষ্যতের পথ-নির্ণয়ে সহায়তা করিবে। এই হিসাবে গ্রন্থের এই অংশ পূৰ্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়াই মনে করি। পাকিস্তান সৃষ্টির পূর্ব্বেই গ্রন্থের এই অংশ রচিত হইয়াছিল। সুতরাং আশা করি কেহ ইহাকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার আন্দোলন বা প্রচারকাৰ্য্য বলিয়া মনে করিবেন না।
ভট্টপল্লী-নিবাসী শ্ৰীযুক্ত ভবতোষ ভট্টাচার্য মহাশয় বল্লালসেন-রচিত ব্রতসাগর গ্রন্থের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। এই জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।
গ্রন্থোক্ত অনেক মন্দির, মূর্ত্তি ও চিত্রের প্রতিকৃতি দেওয়া সম্ভবপর হয় নাই। ইহাতে এই সমুদয়ের বর্ণনা হৃদয়ঙ্গম করা কষ্টসাধ্য হইবে। যে সকল পাঠক এই সমুদয় প্রতিকৃতি, দেখিতে চান, তাহারা ঢাকা, রাজসাহী ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালার এবং কলিকাতা ও আশুতোষ যাদুঘরের মুদ্রিত মূর্ত্তি-তালিকা, স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত “Eastern Indian School of Mediaevel Sculpture’, কাশীনাত দীক্ষিতের “Excavations at Pahaarpur’, cat ক্র্যামরিস প্রণীত “Pala and Sena Sculptures of Bengal”. শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী রচিত “Early Sculpture of Bengal” এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত “History of Bengal, Vol. I” প্রভৃতি গ্রন্থে প্রায় সমুদয় শিল্প-নিদর্শনের প্রতিকৃতিই পাইবেন। এই গ্রন্থে বর্ণনার সাহায্যে ঐ সমুদয় গ্রন্থের চিত্রগুলি আলোচনা করিলে, ইংরেজী-অনভিজ্ঞ পাঠকও বাংলার প্রাচীন সভ্যতা ও কৃষ্টির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঁহার অতীত শিল্পকলা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। সাধারণত যে সমুদয় চিত্র সুপরিচিত নহে-যেমন গোবিন্দভিটা ও ময়নামতীর পোড়া-ইট, চট্টগ্রামের বুদ্ধমূর্ত্তি প্রভৃতি-তাহাই অধিকসংখ্যায় এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছি। এই জন্য অনেক অধিকতর সুন্দর কিন্তু সুপরিচিত মূৰ্ত্তি বাদ গিয়াছে।
ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ ১৮, ২৬, ১৫ (খ), ৩০ ও ৩১ সংখ্যক চিত্রের ব্লক ও ৪, ১০, ১৪, ১৬, ২৪, ২৫ সংখ্যক চিত্রের ফটো দিয়াছেন। আশুতোষ যাদুঘর কাশীপুরের সূৰ্য্যমূর্ত্তি এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কোটালিপাড়ার সূৰ্য্যমূৰ্ত্তির ব্লক দিয়াছেন। ইহাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার
৪নং বিপিন লাল রোড
কলিকাতা
চৈত্র ১৩৫৫
.
প্রথম পরিচ্ছেদ : বাংলা দেশ
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : বাঙ্গালী জাতি
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : প্রাচীন ইতিহাস
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : গুপ্ত-যুগ
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : অরাজকতা ও মাৎস্যন্যায়
যষ্ঠ পরিচ্ছেদ : পালসাম্রাজ্য
সপ্তম পরিচ্ছেদ : পালসাম্রাজ্যের পতন
অষ্টম পরিচ্ছেদ : দ্বিতীয় পালসাম্রাজ্য
নবম পরিচ্ছেদ : তৃতীয় পালসাম্রাজ্য
দশম পরিচ্ছেদ : পালরাজ্যের ধ্বংস
একাদশ পরিচ্ছেদ : বৰ্ম্মরাজবংশ
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ : সেনরাজবংশ
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ : পাল ও সেনরাজগণের কাল-নির্ণয়
চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ : বাংলার শেষ স্বাধীন রাজ্য
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ : রাজ্যশাসনপদ্ধতি
ষোড়শ পরিচ্ছেদ : ভাষা ও সাহিত্য
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ : প্রথম খণ্ড-ধৰ্ম্মমত
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ : সমাজের কথা
উনবিংশ পরিচ্ছেদ : অর্থনৈতিক অবস্থা
বিংশ পরিচ্ছেদ : শিল্পকলা
একবিংশ পরিচ্ছেদ : বাংলার বাহিরে বাঙ্গালী
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ : বাংলার ইতিহাস ও বাঙ্গালীজাতি
নিবেদনং
বাংলা লিপির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ
০১. বাংলা দেশ – প্রথম পরিচ্ছেদ
প্রথম পরিচ্ছেদ – বাংলা দেশ
নাম ও সীমা, প্রাকৃতিক পরিবর্তন, প্রাচীন জনপদ, বঙ্গ, পুণ্ড্র ও বরেন্দ্রী, রাঢ়া, গৌড়
ভারতবর্ষের প্রায় প্রতি প্রদেশেরই নাম ও সীমা কালক্রমে পরিবর্তিত হইয়াছে। শাসন-কার্যের সুবিধার জন্য এক ইংরেজ আমলেই একাধিকবার বাংলা দেশের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এখন যে ভূখণ্ডকে আমরা বাংলা দেশ বলি, এই শতাব্দীর আরম্ভেও তাহার অতিরিক্ত অনেক স্থান ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। আবার সম্প্রতি বাংলা দেশ দুইভাবে বিভক্ত হইয়া দুইটি বিভিন্ন দেশে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং এই পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক বিভাগের উপর নির্ভর করিয়া বাংলা দেশের সীমা নির্ণয় করা যুক্তিযুক্ত নহে। মোটের উপর, যে স্থানের অধিবাসীরা বা তাহার অধিক সংখ্যক লোক সাধারণত বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলে, তাহাই বাংলা দেশ বলিয়া গ্রহণ করা সমীচীন। এই সংজ্ঞা অনুসারে বাংলার উত্তর সীমার হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত কয়েকটি পার্বত্য জনপদ বাংলার বাহিরে পড়ে। কিন্তু বর্তমান কালের পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ, আসামের অন্তর্গত কাছাড় ও গোয়ালপাড়া এবং বিহারের অন্তর্গত পূর্ণিয়া, মানভূম, সিংহভূম সাঁওতাল পরগণার কতকাংশ বাংলার অংশ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। প্রাচীন হিন্দু যুগেও এই সমুদয় অঞ্চলে একই ভাষার ব্যবহার ছিল কিনা, তাহা সঠিক বলা যায় না। কিন্তু আপাতত আর কোনও নীতি অনুসারে বাংলা দেশের সীমা নির্দেশ করা কঠিন। সুতরাং বর্তমান গ্রন্থে আমরা এই বিস্তৃত ভূখণ্ডকেই বাংলা দেশ বলিয়া গ্রহণ করিব।
প্রাচীন হিন্দু যুগে সমগ্র বাংলা দেশের কোন একটি বিশিষ্ট নাম ছিল না। ইহার ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। উত্তরবঙ্গে পূণ্ড্র ও বরেন্দ্র (অথবা বরেন্দ্রী), পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় ও তাম্রলিপ্তি এবং দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে বঙ্গ, সমতট, হরিকেল ও বঙ্গাল প্রভৃতি দেশ ছিল। এতদ্ভিন্ন উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কতকাংশ গৌড় নামে সুপরিচিত ছিল। এই সমুদয় দেশের সীমা ও বিস্তৃতি সঠিক নির্ণয় করা যায় না, কারণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাহার বৃদ্ধি ও হ্রাস হইয়াছে।
মুসলমান যুগেই সর্বপ্রথম এই সমুদয় দেশে একত্রে বাংলা অথবা বাঙ্গালা এই নামে পরিচিত হয়। এই বাংলা হইতেই ইউরোপীয়গণের ‘বেঙ্গলা’ (Bengala) ও ‘বেঙ্গল’ (Bengal) নামে উৎপত্তি। মুঘল সাম্রাজ্যের যুগে ‘বাঙ্গালা’ চট্টগ্রাম হইতে গর্হি পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আইন-ই-আকবরী প্রণেতা আবুল ফজল বলেন, “এই দেশের প্রাচীন নাম ছিল বঙ্গ। প্রাচীন কালে ইহার রাজারা ১০ গজ উচ্চ ও ২০ গজ বিস্তৃত প্রাকণ্ড ‘আল’ নির্মাণ করিতেন; কালে ইহা হইতেই ‘বাঙ্গাল’ এবং ‘বাঙ্গালা’ নামের উৎপত্তি।” এই অনুমান সত্য নহে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী এবং সম্ভবত আরও প্রাচীন কাল হইতেই বঙ্গ ও বঙ্গাল দুইটি দেশ ছিল এবং অনেকগুলি শিলালিপিতে এই দুইটি দেশের একত্র উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বঙ্গ দেশের নাম হইতে ‘আল’ যোগে অথবা অন্য কোন কারণে বঙ্গাল অথবা বাংলা নামের উদ্ভব হইয়াছে, ইহা স্বীকার করা যায় না। বঙ্গাল দেশের নাম হইতেই যে কালক্রমে সমগ্রদেশের বাংলা এই নামকরণ হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। প্রাচীন বঙ্গাল দেশের সীমা নির্দেশ করা কঠিন, তবে এককালে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের তটভূমি যে ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্তমান কালে পূর্ববঙ্গের অধিবাসীগণকে যে বাঙ্গাল নাম অভিহিত করা হয়, তাহা সেই প্রাচীন বঙ্গাল দেশের স্মৃতিই বহন করিয়া আসিতেছে।
অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে গৌড় ও বঙ্গ এই দুইটি সমগ্র বাংলা দেশের সাধারণ নামস্বরূপ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু হিন্দু যুগে ইহারা বাংলা দেশের অংশ-বিশেষকেই বুঝাইত, সমগ্র দেশের নামস্বরূপ ব্যবহৃত হয় নাই।
২। প্রাকৃতিক পরিবর্তন
উত্তরে হিমালয় পর্বত হইতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সমতলভূমি লইয়া বাংলা দেশ গঠিত। পূর্বে গারো ও লুসাই পর্বত এবং পশ্চিমে রাজমহলের নিকটবতী পর্বত ও অনুচ্চ মালভূমি পর্যন্ত এই সমতলভূমি বিস্তৃত। ক্ষদ্র ও বহৎ বহুসংখ্যক নদনদী এই বিশাল সমতলভূমিকে সুজলা, সুফলা ও শস্যশ্যামলা করিয়াছে। পশ্চিমে গঙ্গা ও পূর্বে ব্রহ্মপুত্র এবং ইহাদের অসংখ্য শাখা, উপশাখা ও উপনদীই বাংলা দেশের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সম্পাদন ও ইহার বিভিন্ন অংশের সীমা নিদেশ করিয়াছে। প্রাচীন হিন্দু যুগে এই সমুদয় নদনদীর গতি ও অবস্থিতি যে অনেকাংশে বিভিন্ন ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ গত তিন চারি শত বৎসরের মধ্যে যে এ বিষয়ে গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছে, বাংলার কয়েকটি বড় বড় নদীর ইতিহাস আলোচনা করিলেই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়ার যায়।
অনুচ্চ রাজমহল পর্বতের পাদদেশ ধৌত করিয়া গঙ্গানদী বাংলা দেশে প্রবেশ করিয়াছে। এইস্থানে পর্বত ও নদীর মধ্যবতী প্রদেশ অতি সঙ্কীর্ণ ; সুতরাং ইহা পশ্চিম হইতে আগত শত্রুসৈন্য প্রতিরোধের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক। এই কারণেই তেলিয়াগঢ়ি ও শিকরাগলি গিরিসঙ্কট পশ্চিম বাংলার আত্মরক্ষার প্রথম প্রাকাররূপে চিরদিন গণ্য হইয়াছে, এবং ইহার অনতিদূরেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গৌড় (লক্ষ্মণাবতী), পাণ্ডুয়া, তাণ্ডা ও রাজমহল প্রভৃতি নগরের পত্তন হইয়াছে।
ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে রাজমহলের পাহাড় অতিক্রম করার পরে গঙ্গা নদীর স্রোত বর্তমান কালের অপেক্ষা অনেক উত্তর দিয়া প্রবাহিত হইত এবং বর্তমান মালদহের নিকটবতী প্রাচীন গৌড় নগর খুব সম্ভবত ইহার দক্ষিণে অবস্থিত ছিল।
বর্তমান কালে প্রাচীন গৌড়ের প্রায় ২৫ মাইল দক্ষিণে গঙ্গানদী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এখন ইহার অধিকাংশ জলরাশিই বিশাল পদ্মানদী দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বহন করে। আর যে ভাগীরথী দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া কলিকাতার নিকট দিয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে, তাহার উপরিভাগ শুষ্কপ্রায়। কিন্তু প্রাচীন কালে গঙ্গানদীর প্রধান প্রবাহ সোজা দক্ষিণে যাইয়া ত্রিবেণীর নিকটে ভাগীরথী, সরস্বতী ও যমুনা—এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া সাগরে প্রবেশ করিত। ভাগীরথী অপেক্ষা সরস্বতী নদীই প্রথমে বড় ছিল। ইহা সপ্তগ্রামের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়া তমলুকের (প্রাচীন তাম্রলিপ্তি) নিকট সমুদ্রে মিশিত এবং রূপনারায়ণ, দামোদর ও সাঁওতাল পরগণার অনেক ছোট ছোট নদী ইহার সহিত সংযুক্ত হইয়া ইহার স্রোত বৃদ্ধি করিত। এই সরস্বতী নদী ক্ষীণ হওয়ার ফলেই প্রথমে তাম্রলিপ্তি ও পরে সপ্তগ্রাম, এই দুই প্রসিদ্ধ বন্দরের অবনতি হয়। ক্রমে ভাগীরথী সরস্বতীর স্থান অধিকার করে, এবং ইহার ফলে প্রথমে হুগলী ও পরে কলিকাতার সমদ্ধি হয়। ভাগীরথীরও অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। এখনকার ন্যায় কলিকাতার পরে পশ্চিমে শিবপরে অভিমুখে না গিয়া শত বৎসর পূর্বেও ইহা সোজা দক্ষিণ দিকে কালীঘাট, বারুইপুর, মগরা প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইত।
কেহ কেহ অনুমান করেন, পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্বে পদ্মা নদীর অস্তিত্বই ছিল না। কিন্তু ইহা সত্য নহে। সহস্ৰাধিক বৎসর পূর্বেও যে পদ্মা নদী ছিল, তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে। বৌদ্ধ চযাপদে * (৪৯ নং) পদ্মাখাল বাহিয়া বাঙ্গাল দেশে যাওয়ার উল্লেখ আছে। ইহা হইতে অনুমিত হয়, হাজার বছর আগে পদ্মা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র নদী ছিল। অসম্ভব নহে যে, প্রথমে খাল কাটিয়া ভাগীরথীর সহিত পূর্বাঞ্চলের নদীগুলির যোগ করা হয়; পরে এই খালই নদীতে পরিণত হয়। কারণ কলিকাতার নীচে গঙ্গা ও সরস্বতীর মধ্যে যে খাল কাটা হয়, তাহাই এখন প্রধান গঙ্গা নদীতে পরিণত হইয়া খিদিরপুরের নিকট দিয়া শিবপর অভিমুখে গিয়াছে, এবং কালীঘাটের নিকট আদিগঙ্গা প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে। সে যাহাই হউক, ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বেই পদ্মা বিশাল আকার ধারণ করে। গত তিন চারিশত বৎসরে পদ্মা নদীর প্রবাহ-পথের বহর পরিবর্তন হইয়াছে এবং তাহার ফলে বহন সমদ্ধ জনপদ ও প্রাচীন কীর্তি বিনষ্ট হইয়াছে। সম্ভবত পূর্বে পদ্মা চলনবিলের মধ্য দিয়া বর্তমান ধলেশ্বরী ও বুড়ীগঙ্গার খাত দিয়া প্রবাহিত হইত। বুড়ীগঙ্গা এই নামটি হয়ত সেই যুগের স্মৃতি বহন করিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পদ্মার নিম্নভাগ বর্তমান কালের অপেক্ষা অনেক দক্ষিণে প্রবাহিত হইত, এবং ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ জিলার মধ্য দিয়া চাঁদপুরের ২৫ মাইল দক্ষিণে দক্ষিণ-সাবাজপুরের উপরে মেঘনার সহিত মিলিত হইত। মহারাজ রাজবল্লভের রাজধানী রাজনগর তখন পদ্মার বামতীরে অবস্থিত ছিল। এই নগরীর নিকট দিয়া কালীগঙ্গা নদী পদ্মা হইতে মেঘনা নদী পর্যন্ত প্রবাহিত হইত। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পদ্মার জলস্রোত এই কালীগঙ্গার খাত দিয়া বহিয়া যাইতে আরম্ভ করে, এবং তাহার ফলে রাজবল্লভের রাজধানী রাজনগর এবং চাঁদরায় ও কেদাররায়ের প্রতিষ্ঠিত অনেক নগরী ও মন্দির ধ্বংস হয়। এই কারণে ইহার নাম হয় কীর্তিনাশা। তারপর পদ্মার আরও পরিবর্তন হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে।
ব্ৰহ্মপুত্র নদ পুরাকালে গারো পাহাড়ের পাশ দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব মুখে গিয়া ময়মনসিংহ জিলার মধুপুর জঙ্গলের মধ্য দিয়া ঢাকা জিলার পূর্বভাগে সোনারগাঁর নিকট ধলেশ্বরী নদীর সহিত মিলিত হইত। নারায়ণগঞ্জের নিকটবতী নাঙ্গলবন্দে প্রাচীন ব্রহ্মপুত্রের শুষ্কপ্রায় খাতে এখনও প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ হিন্দু অষ্টমী স্নানের জন্য সমবেত হয়। বৰ্তমানে ব্ৰহ্মপুত্রের জলপ্রবাহ সোজা দক্ষিণে গিয়া গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই অংশের নাম যমুনা।
তিস্তা (ত্রিস্রোতা) উত্তরবঙ্গের প্রধান নদী। প্রাচীন কালে ইহা জলপাইগুড়ির নিকট দিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া পরে তিনটি বিভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হইত। সম্ভবত এই কারণেই ইহা ত্রিস্রোতা নামে পরিচিত ছিল। পূর্বে করতোয়া, পশ্চিমে পুনর্ভবা এবং মধ্যে আত্ৰেয়ী নদীই এই তিনটি স্রোত। আত্ৰেয়ী নদী চলনবিলের মধ্য দিয়া করতোয়ার সহিত মিলিত হইত। করতোয়া এখন শুষ্কপ্রায়, কিন্তু এককালে ইহা খুব বড় নদী ছিল এবং ইহার তীরে বাংলার প্রাচীন রাজধানী পুণ্ড্রবর্ধন নগরী অবস্থিত ছিল। করতোয়ার জল পবিত্র বলিয়া গণ্য হইত এবং ‘করতোয়ামাহাত্ম্য’ গ্রন্থ এই পণ্য-সলিলা নদীর প্রাচীন প্রসিদ্ধির পরিচায়ক। ১৭৮৭ খৃস্টাব্দে ভীষণ জলপ্লাবনের ফলে ত্রিস্রোতার মূল নদী পূর্বখাত পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণ-পূর্বদিকে অগ্রসর হইয়া ব্ৰহ্মপুত্র নদের সহিত মিলিত হয়। এইরপে বৰ্তমান তিস্তা নদীর সৃষ্টি হয় এবং করতোয়া, পুনর্ভবা ও আত্ৰেয়ী ধ্বংসপ্রায় হইয়া উঠে। প্রাচীন কৌশিকী (বর্তমান কুশী) নদী এককালে সমস্ত উত্তরবঙ্গের মধ্য দিয়া দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত হইয়া ব্ৰহ্মপুত্র নদে মিলিত হইত। ক্রমে পশ্চিমে সরিতে সরিতে ইহা এখন বাংলা দেশের বাহিরে পূর্ণিয়ার মধ্য দিয়া রাজমহলের উপরে গঙ্গানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।
এই সমুদয় সপরিচিত দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যাইবে যে, গত পাঁচ ছয় শত বৎসরের মধ্যে বাংলার নদনদীর স্রোত কত পরিবর্তিত হইয়াছে। ইহার পূর্বে প্রাচীন হিন্দু যুগেও যে অনুরূপে পরিবর্তন হইয়াছে, তাহাও সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু এই পরিবর্তনের কোন বিবরণই আমাদের জানা নাই। সুতরাং সে যুগে এই সমুদয় নদনদীর গতি ও প্রবাহ কিরূপ ছিল, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলা চলে না। হিন্দু যুগের বাংলা দেশের ইতিহাস পাঠকালে একথা সকলকেই মনে রাখিতে হইবে যে, কেবলমাত্র বর্তমান কালের নদনদীর অবস্থানের উপর নির্ভর করিয়া এবিষয়ে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত হইবে না।
নদনদীর গতি ও প্রবাহ ব্যতীত অন্য প্রকার প্রাকৃতিক পরিবর্তনেরও কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। সুন্দরবন অঞ্চল যে এককালে সুসমৃদ্ধ জনপদ ও লোকালয়পূর্ণ ছিল, এরপ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত কোটালিপাড়ার বিল অঞ্চলে যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ নগরী, দুর্গ ও বন্দর ছিল, শিলালিপিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। গঙ্গা, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র নদ উচ্চতর প্রদেশ হইতে মাটি বহন করিয়া দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গের বদ্বীপে যে বিস্তৃত নতুন নতুন ভূমির সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার ফলেও অনেক গুরুতর প্রাকৃতিক পরিবর্তন হইয়াছে। সুতরাং নদনদীর ন্যায় বাংলার স্থলভাগও হিন্দু যুগে এখানকার অপেক্ষা অনেকটা ভিন্ন রকমের ছিল।
——————
* ইহার বিশেষ বিবরণ ষোড়শ পরিচ্ছেদের পঞ্চম ভাগে দ্রষ্টব্য।
৩। প্রাচীন জনপদ
পূর্বেই বলা হইয়াছে, হিন্দু যুগে সমগ্র বাংলা দেশের বিশিষ্ট কোনও নাম ছিল না এবং ইহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। ইহার মধ্যে যে কয়টি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, নিম্নে তাহদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।
বঙ্গ
এই প্রাচীন জনপদ বর্তমান কালের দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গ লইয়া গঠিত ছিল। সাধারণত পশ্চিমে ভাগীরথী, উত্তরে পদ্মা, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এবং দক্ষিণে সমুদ্র ইহার সীমারেখা ছিল; কিন্তু কোনও কোনও সময়ে যে ইহা পশ্চিমে কপিশা নদী ও পূর্বে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার পূর্বতীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহারও প্রমাণ আছে। শিলালিপিতে ‘বিক্রমপুর’ ও ‘নাব্য’—প্রাচীন বঙ্গের এই দুইটি ভাগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বিক্রমপুর এখনও সুপরিচিত। নাব্য সম্ভবত বরিশাল ও ফরিদপুরের জলবহুল নিম্নভূমির নাম ছিল, কারণ এই অঞ্চলে নৌকাই যাতায়াতের প্রধান উপায়।
সমতট ও হরিকেল কখনও সমগ্র বঙ্গ এবং কখনও ইহার অংশ-বিশেষের নামস্বরূপ ব্যবহৃত হইত। হেমচন্দ্র তাঁহার অভিধানচিন্তামণি গ্রন্থে বঙ্গ ও হরিকেল একার্থবোধক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন ; কিন্তু মঞ্জুশ্রীমূলকল্প নামক বৌদ্ধগ্রন্থে হরিকেল, সমতট ও বঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন ভূখণ্ডের নাম। আনুমানিক খৃষ্টীয় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত দুইখানি পুঁথিতে হরিকেল শ্রীহট্টের প্রাচীন নাম বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু জাপানে অষ্টাদশ শতাব্দীতে মাদ্রিত একখানি মানচিত্র অনুসারে হরিকেল তাম্রলিপ্তির (বর্তমান তমলুক) দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। হুয়েংসাং সমতটের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে ইহাকে বঙ্গের সহিত অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। বঙ্গাল দেশও বঙ্গের এক অংশের নামান্তর। ইহার বিষয় পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। চন্দ্রদ্বীপ বঙ্গের অন্তর্গত আর একটি প্রসিদ্ধ জনপদ। ইহা মধ্যযুগের সুপ্রসিদ্ধ ‘বাকলা’ হইতে অভিন্ন এবং বাখরগঞ্জ জিলায় অবস্থিত ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন, প্রাচীন কালে এই স্থান ছাড়াও বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত আরও অনেক ভূখণ্ডের নাম ছিল চন্দ্রদ্বীপ, এবং পূর্বে ইন্দোচীন হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে মাদাগাস্কার পৰ্যন্ত অনেক হিন্দু উপনিবেশ এই নামে অভিহিত হইত। বৃহৎসংহিতায় উপবঙ্গ নামক জনপদের উল্লেখ আছে। ষোড়শ অথবা সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত দিগ্বিজয়প্রকাশ নামক গ্রন্থে যশোহর ও নিকটবতী ‘কানন-সংযুক্ত’ প্রদেশ উপবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।
পুণ্ড্র ও বরেন্দ্রী
পুণ্ড্র একটি প্রাচীন জাতির নাম। ইহারা উত্তরবঙ্গে বাস করিত বলিয়া এই অঞ্চল পুণ্ড্রদেশ ও পুণ্ড্রবর্ধন নামে খ্যাত ছিল। এককালে পুণ্ড্রবর্ধন নামক ভুক্তি (দেশের সবোচ্চ শাসন-বিভাগ) গঙ্গা নদীর পূর্বভাগে স্থিত বর্তমান বাংলা দেশের প্রায় সমস্ত ভূখণ্ডকেই বুঝাইত, অর্থাং রাজসাহী, প্রেসিডেন্সি, ঢাকা ও চট্টগ্রাম—বাংলার ভূতপূর্বে এই চারিটি বিভাগ কোন না কোন সময়ে পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তির অন্তর্গত ছিল। পুণ্ড্রদেশের রাজধানীর নামও ছিল পুণ্ড্রবর্ধন। প্রাচীন কালে ইহা একটি প্রসিদ্ধ নগরী ছিল। বগুড়ার সাত মাইল দূরে অবস্থিত মহাস্থানগড়ই প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর ধংসাবশেষ বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, কারণ মৌর্য যুগের একখানি শিলালিপিতে এই স্থানটি পুণ্ড্রবর্ধন নগরী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।
বরেন্দ্র অথবা বরেন্দ্রী উত্তরবঙ্গের আর একটি সপ্রসিদ্ধ জনপদ। রামচরিত কাব্যে বরেন্দ্রীমণ্ডল গঙ্গা ও করতোয়া নদের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া বণিত হইয়াছে।
রাঢ়া
ভাগীরথীর পশ্চিম তীরস্থিত রাঢ় অথবা রাঢ়াদেশ উত্তর ও দক্ষিণরাঢ়া এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। অজয় নদ এই দুই ভাগের সীমারেখা ছিল। রাঢ়াভূমি দক্ষিণে দামোদর এবং সম্ভবত রপনারায়ণ নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কোনও প্রাচীন গ্রন্থে গঙ্গার উত্তর ভাগও রাঢ়াদেশের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণত রাঢ়াদেশ গঙ্গার দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল। রাঢ়ার অপর একটি নাম সুহ্ম।
রাঢ়ার দক্ষিণে বর্তমান মেদিনীপুর অঞ্চলে তাম্রলিপ্তি ও দণ্ডভুক্তি এই দুইটি দেশ অবস্থিত ছিল। তাম্রলিপ্তি বর্তমান কালের তমলুক এবং দণ্ডভুক্তি সম্ভবত দাঁতন। এই দুইটি ক্ষুদ্র দেশ অনেক সময় বঙ্গ অথবা রাঢ়ার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইত।
গৌড়
গৌড় নামটি সুপরিচিত হইলেও ইহার অবস্থিতি সম্বন্ধে সঠিক কোন ধারণা করা যায় না। পাণিনি-সূত্রে গৌড়পুরের এবং কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্রে গৌড়িক স্বর্ণের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে গৌড় নামক নগরী অথবা দেশের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়; কিন্তু বাংলাদেশের কোন অংশ ঐ যুগে গৌড় নামে অভিহিত হইত, তাহা নির্ণয় করা যায় না। খুব সম্ভবত মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের একটি ক্ষদ্র বিভাগ প্রথমে গৌড়-বিষয় (জিলা) নামে পরিচিত ছিল এবং এই বিষয়টির নাম হইতেই গৌড়দেশ এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে। শিলালিপির প্রমাণ হইতে অনুমিত হয় যে, ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই দেশ প্রায় সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে মুর্শিদাবাদের নিকটবর্তী কর্ণসুবৰ্ণ গৌড়ের রাজধানী ছিল এবং এই দেশের রাজা শশাঙ্ক বিহার ও উড়িষ্যা জয় করিয়াছিলেন। সম্ভবত এই সময় হইতেই গৌড় নামটি প্রসিদ্ধি লাভ করে। প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে রাঢ়াপুরী গৌড়ের অন্তর্গত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মসলমান যুগের প্রারম্ভে মালদহ জিলার লক্ষ্মণাবতী গৌড় নামে অভিহিত হইত। বাংলার পরাক্রান্ত পাল ও সেন রাজগণের ‘গৌড়েশ্বর’ এই উপাধি ছিল। হিন্দুযুগের শেষ আমলে বাংলা দেশ গৌড় ও বঙ্গ প্রধানত এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, অর্থাৎ প্রাচীন রাঢ় ও বরেন্দ্রী গৌড়ের অন্তৰ্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। মসলমান যুগের শেষভাগে গৌড়দেশ সমস্ত বাংলাকেই বুঝাইত।
কাশ্মীরের ইতিহাস রাজতরঙ্গিণীতে পঞ্চগৌড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। কোন কোন গ্রন্থে বঙ্গদেশীয় গৌড়, সারস্বত দেশ (পঞ্জাবের পূর্বভাগ) কান্যকুব্জ, মিথিলা ও উৎকল—এই পাঁচটি দেশ একত্রে পঞ্চগৌড় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সম্ভবত গৌড়েশ্বর ধর্মপালের সাম্রাজ্য হইতেই এই নামের উৎপত্তি।
অষ্টম শতাব্দীতে রচিত অনর্ঘরাঘব নাটকে গৌড়ের রাজধানী চম্পার উল্লেখ আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই চম্পানগরী বর্ধমানের উত্তর-পশ্চিমে দামোদর নদের তীরে অবস্থিত ছিল। কিন্তু অসম্ভব নহে যে, এই চম্পা প্রাচীন অঙ্গদেশের রাজধানী বৰ্তমান ভাগলপরের নিকটবতী প্রসিদ্ধ চাপানগরী হইতে অভিন্ন। কারণ একাদশ শতাব্দীর একখানি শিলালিপিতে অঙ্গদেশ গৌড়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।
০২. বাঙ্গালী জাতি
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ –বাঙ্গালী জাতি
১. বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি
সর্বপ্রথম কোন সময়ে বাংলা দেশে মানুষের বসতি আরম্ভ হয়, তাহা জানিবার কোনো উপায় নাই। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আদি যুগের মানব প্রস্তরনিৰ্মিত যে সমুদয় অস্ত্র ব্যবহার করিত, তাহাই তাহাদের অস্তিত্বের প্রধান প্রমাণ ও পরিচয়। সাধারণত এই প্রস্তরগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। সর্বপ্রাচীন মানুষ প্রথমে যে সমুদয় পাষাণ-অস্ত্র ব্যবহার করিত, তাঁহার গঠনে বিশেষ কোনো কৌশল বা পারিপাট্য ছিল না, পরবর্ত্তী যুগে এই অস্ত্র সকল পালিস ও সুগঠিত হয়। এই দুই যুগকে যথাক্রমে প্রত্নপ্রস্তর ও নব্য প্রস্তর যুগ বলা যায়। নব্য প্রস্তর যুগে মানুষের সভ্যতা বৃদ্ধির আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহারা অগ্নি উৎপাদন করিতে জানিত, মাটি পোড়াইয়া বাসন নির্মাণ করিত এবং রন্ধনপ্রণালীতেও অভ্যস্ত ছিল। এই যুগের বহুদিন পরে মানুষ ধাতুর আবিষ্কার করে। মানুষ প্রথমে সাধারণত তাম্রনির্ম্মিত অস্ত্রের ব্যবহার করিত বলিয়া এই তৃতীয় যুগকে তাম্রযুগ বলা হয়। ইহার পরবর্ত্তী যুগে লৌহ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে মানুষ ক্রমে উন্নততর সভ্যতার অধিকারী হয়।
বাংলা দেশেও আদিম মানবসভ্যতার এইরূপ বিবর্ত্তন হইয়াছিল। কারণ এখানেও-প্রধানত পূর্ব্ব ও পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে-প্রত্ন ও নব্য প্রস্তর এবং তাম্রযুগের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। বাংলা দেশের মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগে পলিমাটিতে গঠিত হইয়াছিল। প্রস্তর ও তাম্রযুগে সম্ভবত বাংলার পার্ব্বত্য সীমান্ত প্রদেশেই মানুষ বসবাস করিতক্রমে তাহারা দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে।
বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী আৰ্য্যগণ যখন পঞ্চনদে বসতি স্থাপন করেন তখন তাঁহার বহুদিন পরেও বাংলা দেশের সহিত তাঁহাদের কোনো ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না। বৈদিক সূত্রে বাংলার কোনো উল্লেখ নাই। ঐতয়ের ব্রাহ্মণে অনাৰ্য্য ও দস্যু বলিয়া যে সমুদয় জাতির উল্লেখ আছে, তাঁহার মধ্যে পুরে নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই পুণ্ড জাতি উত্তরবঙ্গে বাস করিত, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গদেশের নিন্দাসূচক উল্লেখ আছে। বৈদিক যুগের শেষভাগে রচিত বৌধায়ন ধৰ্ম্মসূত্রেও পুণ্ডু ও বঙ্গদেশ বৈদিক কৃষ্টি ও সভ্যতার বহির্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং এই দুই দেশে স্বল্পকালের জন্য বাস করিলেও আৰ্যগণের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে এইরূপ বিধান আছে।
এই সমুদয় উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে বাংলার আদিম অধিবাসীগণ আর্য্যজাতির বংশসম্ভূত নহেন। বাংলা ভাষার বিশ্লেষণ করিয়া পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে আর্য্যগণ এদেশে আসিবার পূর্ব্বে বিভিন্ন জাতি এদেশে বসবাস করিত। নৃতত্ত্ববিদগণও বর্ত্তমান বাঙ্গালীর দৈহিক গঠন পরীক্ষার ফলে এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন।
কিন্তু বাংলার অধিবাসী এই সমুদয় অনাৰ্যজাতির শ্রেণীবিভাগ ও ইতিহাস সম্বন্ধে সুধীগণ একমত নহেন। তাঁহাদের বিভিন্ন মতবাদের বিস্তৃত আলোচনা না করিয়া সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে কিছু বলিলেই যথেষ্ট হইবে।
বাংলা দেশে কোল, শবর, পুলিন্দ, হাঁড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভৃতি যে সমুদয় অন্ত্যজ জাতি দেখা যায়, ইহারাই বাংলার আদিম অধিবাসীগণের বংশধর। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে এবং বাহিরেও এই-জাতীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষার মূলগত ঐক্য হইতে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে এই সমুদয় জাতিই একটি বিশেষ মানবগোষ্ঠীর বংশধর। এই মানবগোষ্ঠীকে ‘অস্ট্রো-এশিয়াটিক অথবা অষ্ট্রিক’ এই সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কেহ কেহ ইহাদিগকে ‘নিষাদ জাতি’ এই আখ্যা দিয়াছেন। ভারতবর্ষের বাহিরের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায় এই জাতির সংখ্যা এখনো খুব বেশী।
নিষাদ জাতির পরে আরও কয়েকটি জাতি এদেশে আগমন করে। ইহাদের একটির ভাষা দ্রাবিড় এবং আর একটির ভাষা ব্ৰহ্ম-তিব্বতীয়। ইহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না।
এই সমুদয় জাতিকে পরাভূত করিয়া বাংলা দেশে যাঁহারা বাস স্থাপন করেন, এবং যাহাদের বংশধরেরাই প্রধানত বর্ত্তমানে বাংলার ব্রাহ্মণ, বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতি সমুদয় বর্ণভুক্ত হিন্দুর পূর্ব্বপুরুষ, তাঁহারা যে বৈদিক আর্য্যগণ হইতে ভিন্নজাতীয় ছিলেন, এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে কোনো মতভেদ নাই। রিজলী সাহেবের মতে, মোঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে প্রাচীণ বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব হইয়াছিল। কিন্তু এই মত এখন পরিত্যক্ত হইয়াছে। কোনো কোনো মোঙ্গোলীয় পার্ব্বত্য জাতি বাংলায় উত্তর ও পূর্ব্ব সীমান্তে বাস স্থাপন করিয়াছে কিন্তু এতদ্ব্যতীত প্রাচীন বাঙ্গালী জাতিতে যে মোঙ্গোলীয় রক্ত নাই, ইহা একপ্রকার সর্ব্ববাদীসম্মত। আর দ্রাবিড় নামে কোনো পৃথক জাতির অস্তিত্বই পণ্ডিতগণ এখন স্বীকার করেন না।
মস্তিষ্কের গঠনপ্রণালী হইতেই নৃতত্ত্ববিদগণ মানুষের জাতি নির্ণয় করিয়া থাকেন। মস্তিষ্কের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত অনুসারে যে সমুদয় শ্রেণীবিভাগ কল্পিত হইয়াছে, তাঁহার মধ্যে প্রধান দুইটির নাম ‘দীর্ঘ-শির’ (Dolichocephalic) ও ‘প্রশস্ত-শির’ (Brachycephalic) বৈদিক আর্য্যগণ যে যে প্রদেশে প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন, সেখানকার সকল শ্রেণীর হিন্দুগণ দীর্ঘ-শির। কিন্তু বাংলার সকল শ্ৰেণীর হিন্দুগণই প্রশস্ত-শির। কেহ কেহ অনুমান করেন যে পামির ও টাকলামাকান অঞ্চলের অধিবাসী হোমো-আলপাইনাস নামে অভিহিত একজাতীয় লোকই বাঙ্গালীর আদিপুরুষ। ইহাদের ভাষা আৰ্যজাতীয় হইলেও ইহারা বৈদিক ধর্ম্মাবলম্বী আৰ্য্যগণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু সকলে এই মত গ্রহণ করেন নাই।
মস্তিষ্কের গঠনপ্রণালী হইতে নৃতত্ত্ববিদগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বাঙ্গালী একটি স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট জাতি। এমনকি বাংলা দেশের ব্রাহ্মণের সহিত ভারতের অপর কোনো প্রদেশের ব্রাহ্মণের অপেক্ষা বাংলার কায়স্থ, সদোপ, কৈবৰ্ত্ত প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ।
বাংলার প্রাচীন নিষাদ জাতি প্রধানত কৃষিকাৰ্য্য দ্বারা জীবনযাপন করিত এবং গ্রামে বাস করিত। তাহারা নব্য প্রস্তর যুগের লোক হইলেও ক্রমে তাম্র ও লৌহের ব্যবহার শিক্ষা করিয়াছিল। সমতল ভূমিতে এবং পাহাড়ের গায়ে স্তরে স্তরে ধান্য উৎপাদন প্রণালী তাহারাই উদ্ভাবন করে। কলা, নারিকেল, পান, সুপারি, লাউ, বেগুন প্রভৃতি সজি এবং সম্ভবত আদা ও হলুদের চাষও তাহারা করিত। তাহারা গরু চড়াইত না এবং দুধ পান করিত না, কিন্তু মুরগী পালিত এবং হাতীকে পোষ মানাইত। কুড়ি হিসাবে গণনা করা এবং চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি অনুসারে তিথি দ্বারা দিন-রাত্রির মাপ তাহারাই এদেশে প্রচলিত করে।
নিষাদ জাতির পরে দ্রাবিড়ভাষাভাষি ও আপলাইন শ্রেণীভুক্ত এক জাতি বাংলা দেশে বাস ও বাঙ্গালী জাতির সৃষ্টি করে। পরবর্ত্তীকালে তাহারা নবাগত আৰ্যগণের সহিত এমন ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে তাহাদের পৃথক সত্তা ও সভ্যতা সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা করা কঠিন। কিন্তু আৰ্য্য উপনিবেশের পূর্ব্বে ভারতবর্ষের সভ্যতা কিরূপ ছিল, তাঁহার আলোচনা করিলে এই বাঙ্গালী জাতির সভ্যতা সম্বন্ধে কয়েকটি মোটামুটি সিদ্ধান্ত করা যায়। বর্ত্তমানকালে প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের কয়েকটি বিশিষ্ট অঙ্গ-যেমন কৰ্ম্মফল ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস, বৈদিক হোম ও যাগযজ্ঞের বিরোধী পূজাপ্রণালী, শিব, শক্তি ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেব-দেবীর আরাধনা এবং পুরাণবর্ণিত অনেক কথা ও কাহিনী-তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অনেক লৌকিক ব্রত, আচার, অনুষ্ঠান, বিবাহ-ক্রিয়ায় হলুদ, সিন্দুর প্রভৃতির ব্যবহার, নৌকা নিৰ্মাণ ও অন্যান্য অনেক গ্রাম্য শিল্প এবং ধুতি শাড়ি প্রভৃতি বিশিষ্ট পরিচ্ছদ প্রভৃতিও এই যুগের সভ্যতার অঙ্গ বলিয়াই মনে হয়। মোটের উপর আৰ্যজাতির সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বেই যে বর্ত্তমান বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব হইয়াছিল এবং তাহারা একটি উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট সভ্যতার অধিকারী ছিল এই সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়।
.
২. আৰ্য প্রভাব
বৈদিক যুগের শেষভাবে অথবা তাঁহার অব্যবহিত পরেই বাংলা দেশে আৰ্য্য উপনিবেশ ও আৰ্য সভ্যতা বিস্তারের পরিচয় পাওয়া যায়। বৈদিক ধৰ্ম্মসূত্রে বাংলা দেশ আৰ্য্যাবর্তের বাহিরে বলিয়া গণ্য হইলেও মানবধর্ম্মশাস্ত্রে ইহা আৰ্য্যাবর্তের অন্তর্ভুক্ত এবং পুণ্ড জাতি পতিত ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতে কিন্তু পুণ্ডু ও বঙ্গ এই উভয় জাতিই ‘সুজাত’ ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। জৈন উপাঙ্গ পশ্লবণা (প্রজ্ঞাপন) গ্রন্থে আৰ্যজাতির তালিকায় বঙ্গ এবং রাঢ়ের উল্লেখ আছে। মহাভারতের তীর্থযাত্রা অধ্যায়ে করতোয়া নদীর তীর ও গঙ্গা-সাগরসঙ্গম পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। রামায়ণেও সমৃদ্ধ জনপদগুলির তালিকায় বঙ্গের উল্লেখ আছে।
পুরাণ ও মহাভারতে বর্ণিত আছে যে দীর্ঘতমা নামে এক বৃদ্ধ অন্ধ ঋষি যযাতির বংশজাত পূৰ্ব্বদেশের রাজা মহাধাৰ্মিক পণ্ডিতপ্রবর সংগ্রামে অজেয় বলির আশ্রয় লাভ করেন এবং তাঁহার অনুরোধে তাঁহার রাণী সুদেষ্ণার গর্ভে পাঁচটি পুত্র উৎপাদন করেন। ইহাদের নাম অঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড, সুহ্ম ও বঙ্গ। তাহাদের বংশধরেরা ও তাঁহাদের বাসস্থানও ঐ ঐ নামে পরিচিত। অঙ্গ বর্ত্তমান ভাগলপুর, এবং কলিঙ্গ উড়িষ্যা ও তাঁহার দক্ষিণবর্ত্তী ভূভাগ। পু, সুহ্ম ও বঙ্গ যথাক্রমে বাংলার উত্তর, পশ্চিম এবং দক্ষিণ ও পূৰ্ব্বভাগ। সুতরাং এই পৌরাণিক কাহিনী মতে উল্লিখিত প্রদেশগুলির অধিবাসীরা একজাতীয় এবং আৰ্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মিশ্রণে সমুদ্ভূত। এই কাহিনী ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না কিন্তু ইহা মহাভারত ও পুরাণের যুগে বাংলা দেশে আর্য্যজাতির বিশিষ্ট প্রভাব সূচিত করে।
অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলা দেশেও উন্নত সভ্য অধিবাসীর সঙ্গে সঙ্গে আদিম অসভ্য জাতিও বাস করিত। মহাভারতে বাংলার সমুদ্রতীরবর্ত্তী লোকদিগকে ম্লেচ্ছ এবং ভাগবতপুরাণে সুহ্মগণকে পাপাশয় বলা হইয়াছে। আচারাঙ্গ সূত্র নামক প্রাচীন জৈন গ্রন্থেও পশ্চিমবঙ্গবাসীর বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতার উল্লেখ আছে। তখন রাঢ় দেশ বজ্রভূমি ও সুহ্মভূমি এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর পথহীন এই দুই প্রদেশে ভ্রমণ করিবার সময় এখানকার লোকেরা তাঁহাকে প্রহার করে এবং তাহাদের ‘চুঁ চুঁ’ শব্দে উত্তেজিত হইয়া কুকুরগুলিও তাঁহাকে কামড়ায়। জৈন সন্ন্যাসীগণ অতিশয় খারাপ খাদ্য খাইয়া কোনোমতে বজ্রভূমিতে বাস করেন। কুকুর ঠেকাইবার জন্য সর্বদাই তাঁহারা একটি দীর্ঘ দণ্ড সঙ্গে রাখিতেন। জৈন গ্রন্থকার দুঃখ করিয়া লিখিয়াছেন যে রাঢ়দেশে ভ্রমণ অতিশয় কষ্টকর।
আৰ্য্যগণের উপনিবেশের ফলে আৰ্য্যগণের ভাষা, ধর্ম্ম, সামাজিক প্রথা ও সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গ বাংলা দেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রাচীন অনাৰ্য্যভাষা লুপ্ত হইল, বৈদিক ও পৌরাণিক এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম প্রচারিত হইল, বর্ণাশ্রমের নিয়ম অনুসারে সমাজ গঠিত হইল-এককথায় সভ্যতার দিক দিয়াও বাংলা দেশ আর্য্যাবর্তের অংশরূপে পরিণত হইল। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে যখন কোনো প্রবল উন্নত সভ্য জাতি ও দুর্বল অনুন্নত জাতি পরস্পরের সংস্পর্শে আসে, তখন এই শেষোক্ত জাতি নিজের সত্তা হারাইয়া একেবারে প্রথমোক্ত জাতির মধ্যে মিশিয়া যায়। তবে পুরাতন ভাষা, ধর্ম্ম ও আচার-অনুষ্ঠান একেবারে বিলুপ্ত হয় না-নূতনের মধ্য দিয়া পরিবর্তিত আকারে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলা দেশেও এই নীতির অন্যথা হয় নাই। বাংলার প্রাচীন অনাৰ্য্য জাতি সর্বপ্রকারে আৰ্যসমাজে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালীর ‘খোকা-খুকি’ ডাক, বাঙ্গালী মেয়ের শাড়ি-সিন্দুর ও পান-হলুদ ব্যবহার, বাঙ্গালীর কালী-মনসা পূজা ও শিবের গাজন, বাংলার বালাম চাউল প্রভৃতি আজও সেই অনাৰ্য্য যুগের স্মৃতি বহন করিতেছে। ঠিক কোন সময়ে আৰ্য প্রভাব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা সঠিক নির্ণয় করা যায় না। তবে অনুমান হয় যে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দে বা তাঁহার পূর্ব্বেই যুদ্ধযাত্রা, বাণিজ্য ও ধর্ম্ম প্রচার প্রভৃতি উপলক্ষে ক্রমশ বহুসংখ্যক আৰ্য্য এদেশে আগমন ও বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। গুপ্ত সম্রাটগণ এদেশে রাজ্য স্থাপন করার ফলে যে আৰ্য্য প্রভাব বাংলায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশে গুপ্তযুগের, অর্থাৎ পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দের যে কয়খানি তাম্রশাসন ও শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে আৰ্যগণের ধর্ম্ম ও সামাজিক রীতিনীতি এই সময় বাংলায় দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ধর্ম্ম ও সমাজ প্রসঙ্গে পরবর্ত্তী কয়েকটি পরিচ্ছেদে এ বিষয়ে আলোচনা করা যাইবে। কিন্তু এই যুগে আর্য্য প্রভাবের আরও যে কয়েকটি পরিচয় পাওয়া যায়, নিম্নে তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে।
উপরোক্ত তাম্রশাসন ও শিলালিপিতে শহর ও গ্রামবাসী বহুসংখ্যক বাঙ্গালীর নাম পাওয়া যায়। এই নামগুলি সাধারণত কেবলমাত্র একটি শব্দে গঠিত-যেমন দুর্লভ, গরুড়, বন্ধুমিত্র, ধৃতিপাল, চিরাতদত্ত প্রভৃতি। এই সমুদয় নামের শেষে চট্ট, বর্ম্মণ, পাল, মিত্র, দত্ত, নন্দী, দাস, ভদ্র, দেব, সেন, ঘোষ, কুণ্ড প্রভৃতি বর্ত্তমানে বাংলায় ব্যবহৃত অনেক পদবী দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলি তখন যে নামের অংশমাত্র ছিল অথবা বংশানুক্রমিক পদবীরূপে ব্যবহৃত হইত, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কিন্তু মোটের উপর এই নামগুলি যে আৰ্য প্রভাবের পরিচায়ক, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।
বাংলার গ্রাম ও নগরীর নামেও যথেষ্ট আৰ্য্য প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। পুণ্ড্রবর্দ্ধন, কোটিবর্ষ, পঞ্চনগরী, চণ্ডগ্রাম, কৰ্ম্মান্তবাসক, স্বচ্ছন্দপাটক, শীলকুণ্ডু, নব্যাবকাশিকা, পলাশবৃন্দকে প্রভৃতি বিশুদ্ধ আৰ্য্য নাম। অনাৰ্য্য নামকে সংস্কৃতে রূপান্তরিত করা হইয়াছে এরূপ বহু দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়-যথা খাড়াপাড়া, গোষাট পুঞ্জক প্রভৃতি। প্রাচীন অনাৰ্য্য নামেরও অভাব নাই যেমন ডোঙ্গা, কণামোটিকা ইত্যাদি। এই সমুদয় জনপদ-নামের আলোচনা করিলেও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে আর্য্য সভ্যতা বাঙ্গালীর সমাজে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।
০৩. প্রাচীন ইতিহাস
তৃতীয় পরিচ্ছেদ –প্রাচীন ইতিহাস
গুপ্তযুগের পূর্ব্বে প্রাচীন বাংলার কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন করার উপাদান এখন পর্য্যন্ত আমরা পাই নাই। ভারতীয় ও বিদেশীয় সাহিত্যে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উক্তি হইতে আমরা ইহার সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ পাই, কিন্তু কেবলমাত্র এইগুলির সাহায্যে সন তারিখ ও ঘটনাসম্বলিত কোনো ইতিহাস রচনা সম্ভবপর নহে।
সিংহলদেশীয় মহাবংশ নামক পালি গ্রন্থে নিম্নলিখিত আখ্যানটি পাওয়া যায়।
বঙ্গদেশের রাজা কলিঙ্গের রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের কন্যা মগধ যাইবার পথে লাঢ় (রাঢ়) দেশে এক সিংহ কর্ত্তৃক অপহৃত হন এবং ঐ সিংহের গুহায় তাঁহার সীহবাহু (সিংহবাহু) নামে এক পুত্র ও সীহসীবলী নামে এক কন্যা জন্মে। পুত্রকন্যাসহ তিনি পলাইয়া আসিয়া বঙ্গদেশের সেনাপতিকে বিবাহ করেন। কালক্রমে বঙ্গরাজ্যের মৃত্যু হইলে অপুত্রক রাজার মন্ত্রীগণ সীহবাহুকেই রাজা হইতে অনুরোধ করেন কিন্তু তিনি তাঁহার মাতার স্বামীকে রাজপদে বরণ করিয়া রাঢ়দেশে গমন করেন। এখানে তিনি সীহপুর নামক নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজ্য স্থাপন করেন এবং সীহসীবলীকে বিবাহ করেন। তাঁহার বহু পুত্র জন্মে। তাহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠের নাম ছিল বিজয়।
বিজয় কুসঙ্গীদের সঙ্গে মিশিয়া রাজ্যে নানারকম অত্যাচার করিত। রাজা তাঁহার চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করিলেন কিন্তু কোনো ফল হইল না। অবশেষে বিজয় ও তাঁহার সাত শত সঙ্গীর মাথা অর্ধেক মুড়াইয়া স্ত্রী-পুত্রসহ এক জাহাজে চড়াইয়া তিনি তাহাদিগকে সমুদ্রে ভাসাইয়া দিলেন। তাহারা লঙ্কাদ্বীপে পৌঁছিল।
ভগবান বুদ্ধের নির্বাণলাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটে। ভবিষ্যতে লঙ্কাদ্বীপে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য বুদ্ধের আদেশে শত্রু (ইন্দ্র) বিজয়কে রক্ষা করিবার ভার নিলেন। বিজয় লঙ্কাদ্বীপের যক্ষগণকে পরাস্ত করিয়া রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বঙ্গদেশ হইতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডুবাসুদেব লঙ্কার রাজা হন। এইরূপে লঙ্কাদ্বীপে বাঙ্গালী রাজবংশ পুরুষানুক্রমে রাজত্ব করে। সিংহবাহুর নাম অনুসারে লঙ্কাদ্বীপের নাম হইল সিংহল।
এই কাহিনী ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। বুদ্ধের জীবনকালে বাঙ্গালীরা সমুদ্র পার হইয়া সুদূর সিংহল অথবা লঙ্কাদ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, ইহার অন্য কোনো প্রমাণ নাই। সুতরাং সহস্র বৎসর পরে রচিত মহাবংশের অলৌকিক ঘটনাপূর্ণ কাহিনী বিশ্বাস করা কঠিন। বঙ্গদেশের সহিত লঙ্কাদ্বীপের কোনো রাজনৈতিক সম্বন্ধ থাকা বিচিত্র নহে। কিন্তু তাহা কবে কী আকারে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা সঠিক জানিবার কোনো উপায় নাই।
মহাভারতে বাংলা দেশের কয়েকটি রাজ্যের কথা আছে। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত রাজগণের মধ্যে বঙ্গরাজ সমুদ্রসেনের পুত্র ‘প্রতাপবান’ চন্দ্রসেন, পৌণ্ড্ররাজ বাসুদেব এবং তাম্রলিপ্তির রাজার উল্লেখ আছে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠানকালে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার নিকট ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে বঙ্গ, পুণ্ডু ও কিরাতদেশের অধিপতি পৌণ্ড্রক বাসুদেব বলসমন্বিত ও লোকবিশ্রুত এবং সম্রাট জরাসন্ধের অনুগত। জরাসন্ধের মৃত্যুর পর কর্ণকলিঙ্গ, অঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ডু ও বঙ্গদেশ এক যুক্তরাষ্ট্রের অধীনে আনয়ন করেন। ভীমসেন দিগ্বিজয় উপলক্ষে কৌশিকী নদের তীরবর্ত্তী প্রদেশের রাজা এবং পৌণ্ড্রক বাসুদেব এই দুই মহাবীরকে পরাজিত করিয়া বঙ্গরাজ সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেনকে পরাভূত করেন এবং সুহ্ম তাম্রলিপ্তি, কৰ্বট প্রভৃতি রাজ্য ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী ম্লেচ্ছগণকে জয় করেন। পৌণ্ড্রক বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হন এবং বঙ্গ ও পুণ্ড উভয় দেশই পাণ্ডবগণের অধীনতা স্বীকার করে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে বঙ্গরাজ দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে অতুল সাহস ও পরাক্রমের পরিচয় দেন।
এই সমুদয় আখ্যান হইতে অনুমিত হয় যে মহাভারত রচনার যুগে-এমনকি তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই-বাংলা দেশ অনেকগুলি খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। কখনো কখনো কোনো পরাক্রান্ত রাজা ইহার দুই-তিনটি একত্র করিয়া বিশাল রাজ্য স্থাপন করিতেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের সহিত ও বাংলার রাজগণের রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিল এবং তাঁহাদের শৌর্য্য ও বীর্যের খ্যাতি বাংলার বাহিরেও বিস্তৃত ছিল।
অঙ্গরাজ কর্ণের অধীনে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অধিকাংশ ভাগ মিলিয়া একটি বিশাল রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল-মহাভারতের এই উক্তি কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা বলা কঠিন। কিন্তু খৃ. পূ. ৩২৭ অব্দে যখন আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন যে বাংলা দেশে এইরূপ একটি পরাক্রান্ত রাজ্য ছিল, সমসাময়িক গ্রিক লেখকগণের বর্ণনা হইতে তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়। গ্রীকগণ গণ্ডরিডাই অথবা গঙ্গরিডই নামে যে এক পরাক্রান্ত জাতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহারা যে বঙ্গদেশের অধিবাসী, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কোনো কোনো লেখক গঙ্গা নদীকে এই দেশের পূর্ধ্বসীমা এবং কেহ কেহ ইহার পশ্চিম সীমারূপে বর্ণনা করিয়াছেন। প্লিনি বলেন যে, গঙ্গা নদীর শেষভাগ এই রাজ্যের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই সমুদয় উক্তি হইতে পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গঙ্গা নদীর যে দুইটি স্রোত এখন ভাগীরথী ও পদ্মা বলিয়া পরিচিত, এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে গঙ্গরিডই জাতির বাসস্থান ছিল।
এই গঙ্গরিডই জাতি সম্বন্ধে একজন গ্রীক লিখিছেন : ভারতবর্ষে বহু জাতির বাস। তন্মধ্যে গঙ্গরিডই জাতিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (অথবা সৰ্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী)। ইহাদের চারি সহস্র বৃহত্যায় সুসজ্জিত রণহস্তী আছে, এই জন্যই অপর কোনো রাজা এই দেশ জয় করিতে পারেন নাই। স্বয়ং আলেকজাণ্ডারও এই সমুদয় হস্তীর বিবরণ শুনিয়া এই জাতিকে পরাস্ত করিবার দুরাশা ত্যাগ করেন।
গ্রীকগণ প্রাসিয়য় নামক আর এক জাতির উল্লেখ করেন। ইহাদের রাজধানীর নাম পালিবোথরা (পাটলিপুত্র-বর্ত্তমান পাটনা) এবং ইহারা গঙ্গরিডই দেশের পশ্চিমে বাস করিত। এই দুই জাতির পরস্পর সম্বন্ধ কী ছিল, গ্রীক লেখকগণ সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকাংশ প্রাচীন লেখকই বলিয়াছেন যে এই দুইটি জাতি গঙ্গরিডইর রাজার অধীনে ছিল এবং তাঁহার রাজ্য পাঞ্জাবের অন্তর্গত বিপাশা নদীর তীর হইতে ভারতষের পূর্ব্ব সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্লুতর্ক একস্থলে এই দুই জাতিকে গঙ্গরিডই রাজার অধীন এবং আর একস্থলে দুই জাতির পৃথক রাজার উল্লেখ করিয়াছেন।
অধিকাংশ গ্রীক লেখকের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া মোটের উপর এই সিদ্ধান্ত করা অসমীচীন হইবে না যে, যে সময়ে আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, সেই সময়ে বাংলার রাজ মগধাদি দেশ জয় করিয়া পাঞ্জাব পৰ্য্যন্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। গ্রীক ও লাতিন লেখকগণ এই রাজার যে নাম ও বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে অনেকেই অনুমান করেন যে ইনি পাটলিপুত্রের নন্দবংশীয় কোনো রাজা। ইহা সত্য হইলেও পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধী নহে। কারণ নন্দরাজা বাংলা হইতে গিয়া পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থাপন করিবেন, ইহা অসম্ভব নহে। পরবর্ত্তীকালে বাঙ্গালী পালরাজগণও তাহাই করিয়াছিলেন। পুরাণে নন্দরাজবংশ শূদ্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইহাও পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের সপক্ষে। কারণ বাংলা দেশ বহুকাল পর্য্যন্ত আৰ্য সভ্যতার বহির্ভূত ছিল এবং ইহার অধিবাসী আৰ্য্য ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে শূদ্র বলিয়া বিবেচিত হইবেন ইহাই খুব স্বাভাবিক। অবশ্য নন্দরাজা বাঙ্গালী ছিলেন, ইহা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কিন্তু এই সময় যে বাংলার রাজাই সমধিক শক্তিশালী ছিলেন, প্রাচীন গ্রীক লেখকগণের উক্তি হইতে তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়-এবং যখন ইহার অব্যবহিত পরেই শূদ্র নন্দরাজকে আর্য্যাবর্তের সাৰ্বভৌম রাজারূপে দেখিতে পাই, তখন তিনিই যে এই বাঙ্গালী রাজা এরূপ মত গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। অন্যথা স্বীকার করিতে হয় যে সহসা প্রবল গঙ্গরিডই রাজত্বের লোপ হইয়া নন্দরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল। আলেকজাণ্ডারের ভারতে অবস্থানকালেই এই গুরুতর পরিবর্ত্তন হয়, অথচ সমসাময়িক লেখকগণ ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিলেন না অথবা জানিয়াও উল্লেখ করিলেন না এরূপ অনুমান করা কঠিন।
যদি পাটলিপুত্রের নন্দরাজ ও যবন লেখকগণ বর্ণিত গঙ্গরিডইর রাজা অভিন্ন বলিয়া ধরা যায়-তাহা হইলে খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দী বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবময় যুগ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই মতবাদ গ্রহণ না করিলেও ৩২৭ খ্র. পূ. বাংলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। কারণ, বঙ্গ ও মগধ এই যুক্তরাষ্ট্রের স্থাপনা ও আর্য্যাবর্তে তাঁহার সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা একটি মহৎ কীর্তি। অঙ্গাধিপ কর্ণ সম্ভবত যাহার সূচনা করেন এবং সহস্রাধিক বৎসর পরে শশাঙ্ক ও ধর্ম্মপালের অধীনে যাহার পুনরাবৃত্তি হয়, মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পূর্ব্বে অজ্ঞাতনামা বাংলা দেশের এক রাজা বাহুবলে সেই অপূৰ্ব্ব কীৰ্ত্তি অর্জন করিয়া বিশ্ববিজয়ী যবনবীর আলেকজাণ্ডারের বিস্ময় সম্ভ্রম ও আশঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় বিদেশীয় লেখকগণের কয়েকটি সম্ভমসূচক উক্তি ব্যতীত ইহার পরবর্ত্তী যুগের বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না। বাংলার এই অন্ধকারময় যুগে বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন, গ্রীক শক পুতুব কুষাণ প্রভৃতি বিদেশী জাতির আক্রমণ, দাক্ষিণাত্যে শাতবাহন রাজ্যের অভ্যুদয় এবং আর্য্যাবর্তে বহু খণ্ডাজ্যের উদ্ভব হয়। বাংলা দেশ সম্ভবত মৌৰ্য্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং হয়ত কুষাণ রাজও ইহার কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কোনো সংবাদ জানা যায় না। আলেকজাণ্ডারের অভিযানের চারি পাঁচশত বৎসর পরে লিখিত পেরিপ্লাস গ্রন্থ ও টলেমীর বিবরণ হইতে আমরা জানিতে পারি যে খৃষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে বাংলায় স্বাধীন গঙ্গরিডই রাজ্য বেশ প্রবল ছিল এবং গঙ্গাতীরবর্ত্তী গঙ্গে নামক নগরী ইহার রাজধানী ছিল। এই গঙ্গে নগরী একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল, এবং বাংলার সূক্ষ্ম মসলিন কাপড় এখান হইতে সুদূর পশ্চিম দেশে রপ্তানি হইত। এই সংবাদটুকু ছাড়া খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বে ও পরের তিন শত-মোট ছয় শত বৎসরের বাংলার ইতিহাস নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণ যে গঙ্গরিডই জাতির সাম্রাজ্য ও ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, মহাকবি ভার্জিল যে জাতির শৌর্য-বীর্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন এবং পঞ্চ শতাধিক বৎসর যাঁহারা বাংলা দেশে রাজত্ব করিয়াছেন-এদেশীয় পুরাণ বা অন্য কোনো গ্রন্থে সে জাতির কোনোই উল্লেখ নাই।
০৪. গুপ্ত-যুগ
চতুর্থ পরিচ্ছেদ –গুপ্ত-যুগ
১. গুপ্ত-শাসন
খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তবংশীয় রাজগণ ভারতে বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই বংশের আদিপুরুষ শ্রীগুপ্ত খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষে অথবা চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে কোনো ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার পৌত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্ত প্রপৌত্র সমুদ্রগুপ্ত বহু দেশ জয় করিয়া একটি বিরাট সাম্রাজ্য গঠন করেন। এই সাম্রাজ্য ক্রমে বঙ্গদেশ হইতে কাঠিয়াবার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়।
আদিম গুপ্তরাজ্য কোথায় অবস্থিত ছিল, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। অনেক ঐতিহাসিক অনুমান করেন যে শ্রীগুপ্ত মগধে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু চীনদেশীয় পরিব্রাজক ইৎসিং লিখিয়াছেন যে মহারাজ শ্রীগুপ্ত চীনদেশীয় শ্রমণদের জন্য মৃগস্থাপন স্তূপের নিকটে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে মৃগস্থাপন স্কুপ বরেন্দ্রে অবস্থিত ছিল। সুতরাং মহারাজ শ্রীগুপ্ত যে বরেন্দ্রে অথবা তাঁহার সমীপবর্ত্তী প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইৎসিং বর্ণিত এই শ্রীগুপ্তই গুপ্তরাজবংশের আদিপুরুষ। ইৎসিং বলেন যে শ্রীগুপ্ত পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে রাজত্ব করিতেন। তাহা হইলে শ্রীগুপ্তের রাজ্যকাল দ্বিতীয় শতাব্দের শেষভাগে পড়ে। কিন্তু ইৎসিং-কথিত পাঁচশত বৎসর মোটামুটিভাবে ধরিলে তল্লিখিত শ্রীগুপ্তকে গুপ্তরাজগণের আদিপুরুষ বলিয়া গণ্য করা যায় এবং অনেক পণ্ডিতই এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। এই মত অনুসারে বঙ্গদেশের এক অংশ আদিম গুপ্তরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে গুপ্তগণ বাঙ্গালী ছিলেন এবং প্রথমে বাংলা দেশেই রাজত্ব করিতেন। কিন্তু ইহার সমর্থক কোনো প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।
প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্ত যখন বিশাল গুপ্তসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তখন বাংলা দেশে কতকগুলি স্বাধীন রাজ্য ছিল। বাঁকুড়ার নিকটবর্ত্তী সুসুনিয়া নামক স্থানে পৰ্বতগাত্রে ক্ষোদিত একখানি লিপিতে পুষ্করণের অধিপতি সিংহবর্ম্মা ও তাঁহার পুত্র চন্দ্রবর্ম্মার উল্লেখ আছে। সুসুনিয়ার ২৫ মাইল উত্তর-পূৰ্ব্বে দামোদর নদের দক্ষিণ তটে পোর্ণা নামে একটি গ্রাম আছে। এখানে খুব প্রাচীনকালের মূর্ত্তি ও অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া গিয়াছে। খুব সম্ভবত ইহাই সিংহবর্ম্মা ও চন্দ্রবর্ম্মার প্রাচীন রাজধানী পুষ্করণের ধ্বংসাবশেষ। চন্দ্রবর্ম্মার রাজ্য কত দূর বিস্তৃত ছিল বলা যায় না। ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কোটালিপাড়ায় চন্দ্রবর্ম্মকোট নামক একটি দুর্গ ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর শিলালিপিতে ইহার উল্লেখ আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে উল্লিখিত চন্দ্ৰবৰ্ম্মার নাম অনুসারেই এই দুর্গের ঐরূপ নামকরণ হইয়াছিল। এই মত অনুসারে চন্দ্রবর্ম্মার রাজ্য বাঁকুড়া হইতে ফরিদপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সমুদ্রগুপ্ত যে সমুদয় রাজাকে পরাজিত করিয়া আৰ্য্যাবর্তে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম চন্দ্রবর্ম্মা। খুব সম্ভবত ইনিই পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্ম্মা এবং ইহাকে পরাজিত করিয়াই সমুদ্রগুপ্ত পশ্চিম ও দক্ষিণ বাংলা অধিকার করেন। বাংলা দেশের উত্তর ভাগ সম্ভবত গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কারণ সমুদ্রগুপ্তের শিলালিপিতে কামরূপ (বর্ত্তমান আসাম) গুপ্তসাম্রাজ্যের সীমান্তস্থিত করদরাজ্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে।
প্রাচীন দিল্লীতে কুতবমিনারের নিকটে একটি লৌহস্তম্ভ আছে। এই স্তম্ভগাত্রে ক্ষোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে চন্দ্র নামক একজন রাজা বঙ্গের সম্মিলিত রাজশক্তিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই চন্দ্র কে এবং কোথায় রাজত্ব করিতেন, তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কাহারও কাহারও মতে, তিনি গুপ্তসম্রাট প্রথম অথবা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। প্রথমোক্ত অনুমান স্বীকার করিলে বলিতে হয় যে সমুদ্রগুপ্তের পূর্ব্বেই তাঁহার পিতা বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় অনুমান অনুসারে সমুদ্রগুপ্তের বঙ্গ জয়ের পরেও তাঁহার পুত্রকে আবার বঙ্গদেশ জয় করিতে হইয়াছিল। খুব সম্ভবত লৌহস্তম্ভে উল্লিখিত রাজা চন্দ্র গুপ্তবংশীয় সম্রাট নহেন। এ সম্বন্ধে অন্য যে সমুদয় মতবাদ প্রচলিত তাঁহার সবিস্তারে উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই। কিন্তু রাজা চন্দ্র যিনিই হউন, দিল্লীর স্তম্ভলিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে গুপ্তযুগের প্রাক্কালে বঙ্গে একাধিক স্বাধীন রাজ্য ছিল এবং আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজন হইলে তাহারা সম্মিলিত হইয়া বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিত।
সমতট প্রথমে করদরাজ্য হইলেও ক্রমে ইহা গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং সমস্ত বাংলা দেশই পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্তসাম্রাজ্যের অংশমাত্র ছিল। উত্তরবঙ্গে এই যুগের কয়েকখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলি হইতে জানা যায় যে, বঙ্গদেশের এই অংশ পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তি নামক বিভাগের অন্ত ভুক্ত এবং গুপ্তসম্রাট কর্ত্তৃক নিযুক্ত এক শাসনকর্ত্তার অধীনে ছিল। এই ভুক্তি বা বিভাগ কতকগুলি বিষয় বা জেলায় বিভক্ত ছিল। ৫৪৪ খৃষ্টাব্দে গুপ্তবংশীয় সম্রাট স্বীয় পুত্রকে এই ভুক্তির শাসনকর্ত্তার পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ৫০৭ অব্দে পূৰ্ব্ববঙ্গ অথবা সমতট মহারাজ বৈন্যগুপ্ত শাসন করিতেন। তাঁহার রাজধানী ছিল ক্রীপুর। তিনি পরে নিজ নামে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন এবং মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গুপ্তবংশীয় ছিলেন এবং প্রথমে বঙ্গের শাসনকর্ত্তা হইলেও পরে গুপ্তসাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গে গুপ্তরাজাগণের শাসনপ্রণালী কিরূপ ছিল, তাহা জানা যায় না।
.
২. স্বাধীন বঙ্গরাজ্য
অন্তর্বিদ্রোহ ও হূণজাতির পুনঃপুন আক্রমণের ফলে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে গুপ্তসম্রাটগণ হীনবল হইয়া পড়েন। এই সময়ে যশোধর্ম্মণ নামে এক দুর্ধর্ষ বীর সমগ্ৰ আৰ্য্যাবৰ্ত্তে আপনার প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁহার জয়স্তম্ভে উল্লিখিত হইয়াছে যে তিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে পশ্চিমে আরবসাগর এবং উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে মহেন্দ্রগিরি (গঞ্জাম জিলায় অবস্থিত) পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রশস্তিকারের এই উক্তি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে বাংলা দেশও তাঁহার অধীনস্থ ছিল, একথা স্বীকার করিতে হয়। যশোধর্ম্মণের রাজ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী না হইলেও ইহার ফলে গুপ্তসাম্রাজ্যের ধ্বংস আরম্ভ হয়। এই সময় এবং সম্ভবত এই সুযোগে দক্ষিণ ও পূৰ্ব্ববঙ্গ গুপ্তসম্রাটগণের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া একটি পরাক্রান্ত স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হয়। কোটালিপাড়ার পাঁচখানি এবং বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত মল্লসারুলে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসনে এই স্বাধীন বঙ্গরাজ্যর কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। এই ছয়টি তাম্রশাসনে গোপচন্দ্র, ধৰ্ম্মাদিত্য ও সমাচারদেব এই তিনজন রাজার নাম পাওয়া যায়। ইহারা সকলেই মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সমাচারদেবের স্বর্ণমুদ্রা এবং নালন্দার ধ্বংসাবশেষ মধ্যে তাঁহার নামাঙ্কিত শাসনমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং তাহারা যে বেশ শক্তিশালী স্বাধীন রাজা ছিলেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। সমগ্র দক্ষিণ এবং পূৰ্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গের অন্তত কতকাংশ এই স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
এই যুগের আরও কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা বাংলা দেশের নানা স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্ভবত পূর্ব্বোক্ত স্বাধীন বঙ্গদেশের রাজগণই এগুলি প্রচলিত করিয়াছিলেন। এই সমুদয় মুদ্রায় যে সকল রাজার নাম আছে, তাঁহার মধ্যে মাত্র দুইটি অনেকটা নিশ্চিতরূপে পড়া যায়। একটি পৃথুবীর অপরটি শ্রীসুধন্যাদিত্য।
এই সমুদয় রাজাই একবংশীয় কি না তাহা বলা কঠিন। যে সমুদয় রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে, তাঁহার মধ্যে গোপচন্দ্ৰই সৰ্ব্বপ্রাচীন ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি অন্তত ১৮ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার পর ধৰ্ম্মাদিত্য ও সমাচারদেব যথাক্রমে অন্তত ৩ ও ১৪ বৎসর রাজত্ব করেন। সম্ভবত এই তিনজন রাজা খৃষ্টীয় ৫২৫ হইতে ৫৭৫ অব্দের মধ্যে রাজত্ব করেন। দুঃখের বিষয়, এই রাজাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোনো বিবরণই জানা যায় না। এমনকি তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কী সম্বন্ধ ছিল, তাহাও নির্ণয় করিবার উপায় নাই। তবে তাঁহাদের তাম্রশাসনগুলি পড়িলে মনে হয় যে তাঁহাদের অধীনে স্বাধীন বঙ্গরাজ্য প্রভাব-প্রতিপত্তি ও সমৃদ্ধিশালী ছিল।
কোন সময়ে কিভাবে এই স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের অবসান হয়, তাহা বলা যায়। দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজ কীৰ্ত্তিবৰ্মণ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষপাদে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধ জয় করেন বলিয়া তাঁহার প্রশস্তিকারেরা উল্লেখ করিয়াছেন। চালুক্যরাজের আক্রমণের ফলেই হয়তো বঙ্গরাজ্য দুৰ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তবে খুব সম্ভবত স্বাধীন গৌড়রাজ্যের অভ্যুদয়ই ইহার পতনের প্রধান কারণ।
.
৩. গৌড় রাজ্য
গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের পর পরবর্ত্তী ‘গুপ্তবংশ’ নামে পরিচিত এক বংশের গুপ্ত উপাধিধারী রাজগণ এই সাম্রাজ্যের এক অংশ অধিকার করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কতকাংশ এই রাজবংশের অধীন ছিল। এই সময়ে বাংলা দেশে এই অঞ্চল গৌড় নামে প্রসিদ্ধ হয়। নামত গুপ্তরাজগণের অধীন হইলেও ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে গৌড় একটি বিশিষ্ট জনপদরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তখন মৌখরি বংশ বর্ত্তমান যুক্তপ্রদেশে রাজত্ব করিতেন। এই বংশের পরাক্রান্ত রাজা ঈশানবর্ম্মা সম্বন্ধে তাঁহার একখানি শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে যে তিনি গৌড়গণকে পরাজিত ও বিপর্যস্ত করিয়া তাহাদিগকে সমুদ্রে আশ্রয় লইতে বাধ্য করেন। ইহার অর্থ সম্ভবত এই যে গৌড়ের অধিবাসীগণ সমুদ্রতীরে যাইয়া আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহাতে বাঙ্গালীর নৌবলের সাহায্যে আত্মরক্ষা অথবা সমুদ্র লঙ্নপূৰ্ব্বক অন্য দেশে যাইয়া বাসস্থানের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। সে যাহাই হউক, সমুদ্রের উল্লেখ হইতে মনে হয় যে তখন সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ গৌড়ের অন্তর্গত ছিল।
মৌখরি ও পরবর্ত্তী গুপ্তবংশীয় রাজগণের মধ্যে পুরুষানুক্রমিক বিবাদ চলিতেছিল। ঈশানবর্ম্মা কর্ত্তৃক গৌড় বিজয় এই বিবাদের ইতিহাসে একটি ক্ষুদ্র অধ্যায়মাত্র। গুপ্তরাজগণের শিলালিপি অনুসারে গুপ্তরাজ কুমারগুপ্ত ঈশানবর্ম্মাকে পরাজিত করেন এবং কুমারগুপ্তের পুত্র দামোদরগুপ্ত মৌখরিদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ঈশানবর্ম্মার পরবর্ত্তী মৌখরিরাজ শৰ্ব্ববর্ম্মা ও অবন্তিবর্ম্মা সম্ভবত মগধের কিয়দংশ অধিকার করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহার ফলে গুপ্তরাজগণ মগধ ও গৌড় পরিত্যাগ করিয়া মালবে রাজত্ব করেন। কিন্তু ইহা সত্য হউক বা না হউক, ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে যে গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্তের রাজ্য পূৰ্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। সুতরাং গৌড় ও মগধ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।
অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী এই সংঘর্ষের ফলে এবং উত্তর হইতে তিব্বতীয়দের এবং দক্ষিণ হইতে চালুক্যরাজ্যের আক্রমণে সম্ভবত পরবর্ত্তী গুপ্তরাজগণ হীনবল হইয়া পড়েন এবং এই সুযোগে গৌড়দেশে শশাঙ্ক এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।
.
৪. শশাঙ্ক
বাঙ্গালী রাজগণের মধ্যে শশাঙ্কই প্রথম সাৰ্বভৌম নরপতি। তাঁহার বংশ বা বাল্যজীবন সম্বন্ধে সঠিক কিছুই জানা যায় না। কেহ কেহ মতপ্রকাশ করিয়াছেন যে শশাঙ্কের অপর নাম নরেন্দ্র গুপ্ত এবং তিনি গুপ্তরাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এই মতটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়াই মনে হয়। প্রাচীন রোহিতাশ্বের (রোটাসগড়) গিরিগাত্রে শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক এই নামটি ক্ষোদিত আছে। যদি এই শশাঙ্ক ও গৌড়রাজ শশাঙ্ককে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, শশাঙ্ক প্রথমে একজন মহাসামন্ত মাত্র ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে শশাঙ্ক মৌখরিরাজ্যের অধীনস্থ সামন্তরাজা ছিলেন। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাবে গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্ত মগধ ও গৌড়ের অধিপতি ছিলেন। সুতরাং শশাঙ্ক এই মহাসেনগুপ্তের অধীনে মহাসামন্ত ছিলেন, এই মতই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।
৬০৬ অব্দের পূর্ব্বেই শশাঙ্ক একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী কর্ণসুবর্ণ খুব সম্ভবত মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুরের ছয় মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে রাঙ্গামাটি নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। শশাঙ্ক দক্ষিণে দণ্ডভুক্তি (মেদিনীপুর জেলা), উল্কল, ও গঞ্জাম জেলায় অবস্থিত কোঙ্গোদ রাজ্য জয় করেন। উৎকল ও দণ্ডভুক্তি তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। শৈলোদ্ভব বংশীয় রাজগণ তাঁহার অধীনস্থ সামন্তরূপে কোঙ্গোদ শাসন করিতেন। পশ্চিমে মগধ রাজ্যও শশাঙ্ক জয় করেন। দক্ষিণবঙ্গে যে স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের কথা পূৰ্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, সম্ভবত তাহাও শশাঙ্কের অধীনতা স্বীকার করে। কিন্তু এ সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না।
শশাঙ্কের পূৰ্ব্বে আর কোনো বাঙ্গালী রাজা এইরূপ বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা নাই। কিন্তু শশাঙ্ক ইহাতেই সন্তুষ্ট হন নাই। তিনি গৌড়ের চিরশত্রু মৌখরিদিগকে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।
মৌখরিরাজ গ্রহবর্ম্মা পরাক্রান্ত স্থাণীশ্বরের (থানেশ্বর) রাজা প্রভাকরবর্দ্ধনের কন্যা রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মাও শশাঙ্কের ভয়ে থানেশ্বররাজের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। শশাঙ্কও এই দুই মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য মালবরাজ দেবগুপ্তের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন।
কী কারণে এই দুই দলের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং এই যুদ্ধের প্রথম ভাগের বিবরণ নিশ্চিত জানা যায় না। শশাঙ্ক সম্ভবত প্রথমে বারাণসী অধিকার করিয়া পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন এবং দেবগুপ্তও মালব হইতে সসৈন্যে কান্যকুব্জ (কনৌজ) যাত্রা করেন। ইহার পরবর্ত্তী ঘটনা সম্বন্ধে সমসাময়িক ‘হর্ষচরিত গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায়।
‘থানেশ্বররাজ প্রভাকরবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্দ্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এমন সময় কান্যকুব্জ হইতে দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে মালবের রাজা কান্যকুব্জরাজ গ্রহবর্ম্মাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিয়া রাণী রাজশ্রীকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন এবং থানেশ্বর আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছেন। এই নিদারুণ সংবাদ শুনিয়া রাজ্যবর্দ্ধন কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধনের উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া অবিলম্বে দশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য মাত্র লইয়া ভগিনীর উদ্ধারের নিমিত্ত অগ্রসর হইলেন। পথে মালবরাজের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি মালবকে পরাজিত করিয়া তাঁহার বহু সৈন্য বন্দী করিয়া থানেশ্বরে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কান্যকুজে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই শশাঙ্কের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয়।’
হর্ষচরিত্রের বিভিন্ন স্থানে এই ঘটনার যেরূপ উল্লেখ আছে, তাহাতে মনে হয় যে দেবগুপ্ত কান্যকুব্জ জয় করিয়াই শশাঙ্কের জন্য অপেক্ষা না করিয়া থানেশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। শশাঙ্ক কান্যকুজে পৌঁছিয়া এই সংবাদ শুনিয়া দেবগুপ্তের সাহায্যে অগ্রসর হন। কিন্তু এই দুই মিত্রশক্তি মিলিত হইবার পূর্ব্বেই রাজ্যবর্দ্ধন দেবগুপ্তকে পরাস্ত ও নিহত করেন। দেবগুপ্তের ন্যায় রাজ্যবর্দ্ধনও জয়োল্লাসে সমূহ-বিপদের আশঙ্কা না করিয়া নিজের ক্ষুদ্র সৈন্যের কতক বন্দী মালবসৈন্যের সঙ্গে থানেশ্বরে প্রেরণ করেন এবং অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া কান্যকুজের দিকে অগ্রসর হন। সম্ভবত পথে শশাঙ্কের সঙ্গে তাঁহার যুদ্ধ হয় এবং তিনি পরাস্ত ও নিহত হন।
শশাঙ্ক কর্ত্তৃক রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যার কথা আমরা তিনটি বিভিন্ন সূত্রে জানিতে পারি। হর্ষবর্দ্ধনের সভাকবি বাণভট্টের হর্ষচরিত গ্রন্থ, হর্ষবর্দ্ধনের পরম সুহৃদ চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন সাংয়ের কাহিনী, এবং হর্ষবর্দ্ধনের শিলালিপি। বাণভট্ট লিখিয়াছেন যে মিথ্যা উপচারে আশ্বস্ত হইয়া রাজ্যবর্দ্ধন একাকী নিরস্ত্র শশাঙ্কের ভবনে গমন করেন এবং তৎকর্ত্তৃক নিহত হন। রাজ্যবর্দ্ধন কেন এইরূপ অসহায় অবস্থায় শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ করিলেন বাণভট্ট সে সম্বন্ধে একেবারে নীরব। হর্ষচরিতের টীকাকার শঙ্কর লিখিয়াছেন যে শশাঙ্ক তাঁহার কন্যার সহিত বিবাহের প্রলোভন দেখাইয়া রাজ্যবর্দ্ধনকে স্বীয় ভবনে আনয়ন করেন এবং রাজ্যবর্দ্ধন তাঁহার সঙ্গীগণসহ আহারে প্রবৃত্ত হইলে ছদ্মবেশে তাঁহাকে হত্যা করেন। শঙ্কর সম্ভবত চতুর্দ্দশ শতাব্দীর অথবা পরবর্ত্তীকালের লোক। যে ঘটনা বাণভট্ট উল্লেখ করেন নাই হাজার বৎসর পরে শঙ্কর কিরূপে তাঁহার সন্ধান পাইলেন জানি না। কিন্তু তাঁহার বর্ণনার সহিত বাণভট্ট কথিত এ নিরস্ত্রকারী’ রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর কাহিনীর সামঞ্জস্য নাই।
হুয়েন সাং বলেন যে, শশাঙ্ক পুনঃপুন তাঁহার মন্ত্রীগণকে বলিতেন যে সীমান্ত রাজ্যে রাজ্যবর্দ্ধনের ন্যায় ধার্মিক রাজা থাকিলে নিজ রাজ্যের কল্যাণ নাই। এই কথা শুনিয়া শশাঙ্কের মন্ত্রীগণ রাজ্যবর্দ্ধনকে একটি সভায় আমন্ত্রণ করিয়া তাহাকে হত্যা করে। হুয়েন সাংয়ের এই উক্তি কোনোমতেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ রাজ্যবর্দ্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি ধার্মিক বা অধাৰ্মিক ইহা বিচার করিবার এবং এ বিষয়ে পুনঃপুন মন্ত্রীগণকে বলিবার সুযোগ বা সম্ভাবনা শশাঙ্কের ছিল না। অন্যত্র হুয়েন সাং লিখিয়াছেন, “রাজ্যবর্দ্ধনের মন্ত্রীগণের দোষেই রাজ্যবর্দ্ধন শক্তহস্তে নিহত হইয়াছেন-মন্ত্রীরাই ইহার জন্য দায়ী”। বাণভট্ট-কথিত ‘মিথ্যা উপচারে আশ্বস্ত রাজ্যবর্দ্ধনের একাকী নিরস্ত্র শশাঙ্কভবনে গমনের সহিত ইহার সঙ্গতি নাই।
হর্ষবর্দ্ধনের শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে যে সত্যানুরোধে রাজ্যবর্দ্ধন শক্ৰভবনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। এখানে শশাঙ্কের বিশ্বাসঘাতকতার কোনো ইঙ্গিতই নাই।
তিনটি সমসাময়িক বিবরণে একই ঘটনা সম্বন্ধে এই প্রকার বিরোধিতা দেখিলে স্বতই তাঁহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। তারপর ইহাও উল্লেখযোগ্য যে বাণভট্ট ও হুয়েন সাং উভয়েই শশাঙ্কের পরম বিদ্বেষী এবং তাহাদের গ্রন্থের নানা স্থানে শশাঙ্ক সম্বন্ধে অশিষ্ট উক্তি ও অলীক কাহিনীতে এই বিদ্বেষভাব প্রকটিত হইয়াছে। সুতরাং কেবলমাত্র এই দুইজনের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া শশাঙ্ক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া রাজ্যবর্দ্ধনকে হত্যা করিয়াছিলেন, এই মত গ্রহণ করা সমীচীন নহে। যুদ্ধে নিরত দুই পক্ষের পরস্পরের প্রতি অভিযোগ প্রায়শই কত অমূলক বর্ত্তমানকালের দুইটি মহাযুদ্ধে তাঁহার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে শিবাজী কর্ত্তৃক আফজলখানের হত্যার কাহিনী উল্লেখযোগ্য। মহারাষ্ট্র গ্রন্থমতে আফজলখানই বিশ্বাসঘাতক, আবার মুসলমান ঐতিহাসিকেরা শিবাজী সম্বন্ধে ঐ অপবাদ ঘোষণা করেন। শশাঙ্ক সম্বন্ধে গৌড়দেশীয় কোনো লেখকের গ্রন্থ থাকিলে তাহাতে সম্ভবত রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যার সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকম বিবরণই পাওয়া যাইত।
এই প্রসঙ্গে রোম সম্রাট ভ্যালেরিয়ানের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কাহারও মতে, ভ্যালেরিয়ান যখন পারস্যের রাজার সহিত সন্ধির কথাবার্তা চালাইতেছিলেন, তখন পারস্যের রাজা তাঁহাকে আমন্ত্রণ করেন এবং সাক্ষাৎ হইলে বন্দী করেন। অপর মত অনুসারে ভ্যালেরিয়ান অল্প সৈন্য লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং পারস্যরাজের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে এক অবরুদ্ধ দুর্গে অবস্থানকালে স্বীয় বিদ্রোহী সৈন্যের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্য তিনি পলাইয়া পারস্যরাজের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। অসম্ভব নহে যে অনুরূপ কোনো কারণেই রাজ্যবর্দ্ধন শশাঙ্কের বন্দী হইয়াছিলেন। বাণভট্ট নিজেই বলিয়াছেন যে মাত্র দশ সহস্র সৈন্য লইয়া তিনি মালবরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে কতক মালবরাজের সহিত যুদ্ধে হতাহত হইয়াছিল এবং কতক বন্দী মালব সৈন্যসহ থানেশ্বরে প্রেরিত হইয়াছিল। শশাঙ্ক যে দশ সহস্রের অনধিক সৈন্য লইয়া সুদূর কান্যকুজে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। অপরপক্ষে রাজ্যবর্দ্ধন বৌদ্ধ ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে হর্ষবর্দ্ধনের বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি অনুরাগের জন্য তাঁহার প্রজাগণ তাঁহার প্রাণনাশের জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। সুতরাং রাজ্যবর্দ্ধনের মন্ত্রীগণও যে কৌশলে তাঁহার হত্যাসাধনে সহায়তা করিবেন, ইহা একেবারে অবিশ্বাস্য নহে। “রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর জন্য তাঁহার মন্ত্রীগণই দায়ী” হুয়েন সাংয়ের এই উক্তি এই অনুমানের পরিপোষক। যুদ্ধে পরাজয় অথবা মন্ত্রীগণের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে যদি রাজ্যবর্দ্ধন নিহত হইয়া থাকেন, তবে হর্ষবর্দ্ধনের পক্ষীয় লেখক যে এই কলঙ্কের উল্লেখ করিবেন না ইহাই খুব স্বাভাবিক। সুতরাং কেবলমাত্র বাণভট্ট ও হুয়েন সাংয়ের পরস্পরবিরোধী, অস্বাভাবিক, অস্পষ্ট উক্তি এবং অসম্পূর্ণ কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া শশাঙ্ককে বিশ্বাসঘাতক হত্যাকারীরূপে গ্রহণ করা কোনো ক্রমেই যুক্তিসিদ্ধ নহে।
বাণভট্ট বলেন যে রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যার সংবাদ শুনিয়া হর্ষবর্দ্ধন শপথ করিলেন যে যদি নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে তিনি পৃথিবী গৌড়শূন্য করিতে না পারেন, তবে অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। অতঃপর গৌড়রাজের বিরুদ্ধে বিপুল সমর-সজ্জা হইল। হর্ষ সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া পথিমধ্যে শুনিলেন যে তাঁহার ভগ্নী রাজ্যশ্রী কারাগার হইতে পলাইয়া বিন্ধ্যপর্বতে প্রস্থান করিয়াছেন। সুতরাং সেনাপতি ভণ্ডীকে সসৈন্যে অগ্রসর হইতে আদেশ দিয়া তিনি নিজে ভগ্নীর সন্ধানে বিন্ধ্যপর্বতে গমন করিলেন। সেখানে রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করিয়া তিনি গঙ্গাতীরে স্বীয় সৈন্যের সহিত মিলিত হইলেন।
বাণভট্টের গ্রন্থ এখানেই শেষ হইয়াছে। শশাঙ্কের সহিত হর্ষের যুদ্ধের কথা বাণভট্ট কিছুই বলেন নাই। কিন্তু হুয়েন সাং লিখিয়াছেন যে হর্ষ ছয় বৎসর যাবৎ অনবরত যুদ্ধ করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। হর্ষবর্দ্ধন দাক্ষিণাত্যের রাজা পুলকেশীর হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। আর্য্যাবর্তে অন্তত ৬১৯ খৃ. অব্দ পর্য্যন্ত শশাঙ্ক একজন শক্তিশালী রাজা ছিলেন। কারণ ঐ বৎসরে উত্তীর্ণ একখানি তাম্রশাসনে গঞ্জাম জিলাস্থিত কোঙ্গোদের শৈলোববংশীয় রাজা “চতুরুদধিসলিলবীচীমেখলা দ্বীপগিরিপত্তনবতী” বসুন্ধরার অধিপতি মহারাজাধিরাজ শ্রীশশাঙ্কের মহাসামন্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। শশাঙ্ক যে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মগধের অধিপতি ছিলেন হুয়েন সাংয়ের উক্তি হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। কারণ হুয়েন সাংয়ের উক্তি অনুসারে ৬৩৭ খৃষ্টাব্দের অনতিকাল পূৰ্ব্বে শশাঙ্ক গয়ার বোধিবৃক্ষ ছেদন করেন এবং নিকটবর্ত্তী একটি মন্দির হইতে বুদ্ধমূর্ত্তি সরাইতে আদেশ দেন; ইহার ফলে শশাঙ্কের সর্বাঙ্গে ক্ষত হয়, তাঁহার মাংস পচিয়া যায় এবং অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়।
সুতরাং হর্ষবর্দ্ধন তাঁহার কঠোর প্রতিজ্ঞা ও বিরাট যুদ্ধসজ্জা সত্ত্বেও শশাঙ্কের বিশেষ কিছু অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। শশাঙ্কের সহিত তাঁহার কোনো যুদ্ধ হইয়াছিল কি না তাহাও নিশ্চিত জানা যায় না। কেবলমাত্র আমঞ্জুশ্রীমূলকল্প নামক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। এই বৌদ্ধ গ্রন্থখানি খুব প্রাচীন নহে। পুরাণের মতো এই গ্রন্থে ভবিষ্যৎ রাজাদের বিবরণ আছে। কিন্তু কোনো রাজার নামই পুরাপুরি দেওয়া নাই, হয় প্রথম অক্ষর অথবা সমার্থক কোনো শব্দ দ্বারা সূচিত করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না, ইহা মধ্যযুগের কতকগুলি কিংবদন্তীর সমাবেশ মাত্র। এই গ্রন্থোক্ত রাজা ‘সোম’ সম্ভবত শশাঙ্ক এবং তাঁহার শত্রু হকারাখ্য রাজা ও তাঁহার রকারাখ্য জ্যেষ্ঠভ্রাতা যথাক্রমে হর্ষবর্দ্ধন ও রাজ্যবর্দ্ধন। এই অনুমান স্বীকার করিয়া লইলে এই গ্রন্থে আমরা নিম্নোক্ত বিবরণ পাই।
“এই সময়ে মধ্যদেশে বৈশ্যজাতীয় রাজ্যবর্দ্ধন রাজা হইবেন। তিনি শশাঙ্কের তুল্য শক্তিশালী হইবেন। নগ্নজাতীয় রাজার হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইবে। অসাধারণ পরাক্রমশালী তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধন বহু সৈন্যসহ শশাঙ্কের রাজধানী পুণ্ড্রনগরীর বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তিনি দুবৃত্ত শশাঙ্ককে পরাজিত করেন এবং ঐ বৰ্বর দেশে যথোপযুক্ত সম্মান না পাওয়ায় (মতান্তরে ‘পাইয়া’) স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।”
এই উক্তি কত দূর সত্য বলা যায় না। কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেও মাত্র ইহাই প্রমাণিত হয় যে হর্ষবর্দ্ধন শশাঙ্কের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু বিশেষ কোনো সাফল্য লাভ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।
মঞ্জুশ্ৰীমূলকল্প মতে শশাঙ্ক মাত্র ১৭ বৎসর রাজত্ব করেন। কিন্তু ইহা সত্য নহে। শশাঙ্ক ৬.৬ অব্দের পূর্ব্বেই রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন এবং পূৰ্ব্বোদ্ধৃত হুয়েন সাংয়ের উক্তি হইতে প্রমাণিত হয় যে ৬৩৭ অব্দের অনতিকাল পূৰ্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হয়। শশাঙ্কের যে তিনখানি লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাঁহার একখানির তারিখ ৬১৯ অব্দ। খুব সম্ভবত মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত শশাঙ্ক গৌড়, মগধ, দণ্ডভুক্তি, উৎকল ও কোঙ্গোদের অধিপতি ছিলেন।
শশাঙ্ক শিবের উপাসক ছিলেন। হুয়েন সাং তাঁহার বৌদ্ধবিদ্বেষ সম্বন্ধে অনেক গল্প লিখিয়াছেন কিন্তু এগুলি বিশ্বাস করা কঠিন। কারণ হুয়েন সাংয়ের বর্ণনা হইতেই বেশ বোঝা যায় যে শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণে এবং তাঁহার রাজ্যের সৰ্ব্বত্র বৌদ্ধধর্ম্মের বেশ প্রসার ও প্রতিপত্তি ছিল।
বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্কের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। তিনিই প্রথম আৰ্য্যাবর্তে বাঙ্গালীর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন এবং ইহা আংশিকভাবে কাৰ্য্যে পরিণত করেন। প্রতিদ্বন্দ্বী প্রবল মৌখরিরাজশক্তি তাঁহার কূটনীতি ও বাহুবলে সমূলে ধ্বংস হয়। সমগ্র উত্তরাপথের অধীশ্বর প্রবল শক্তিশালী হর্ষবর্দ্ধনের সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া তিনি বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার আধিপত্য বজায় রাখিয়াছিলেন। বাণভট্টের মতো চরিত-লেখক অথবা হুয়েন সাংয়ের মতো সুহৃৎ থাকিলে হয়ত হর্ষবর্দ্ধনের মতোই তাঁহার খ্যাতি চতুর্দিকে বিস্তৃত হইত। কিন্তু অদৃষ্টের নিদারুণ বিড়ম্বনায় তিনি স্বদেশে অখ্যাত এবং অজ্ঞাত; এবং শত্রুর কলঙ্ককালিমাই তাহাকে জগতে পরিচিত করিয়াছে।
০৫. অরাজকতা ও মাৎস্যন্যায়
পঞ্চম পরিচ্ছেদ –অরাজকতা ও মাৎস্যন্যায়
১. গৌড়
শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে আনুমানিক ৬৩৮ অব্দে হুয়েন সাং বাংলা দেশ পরিভ্রমণ করেন। তিনি কজঙ্গল (রাজমহলের নিকট), পুণ্ড্রবর্দ্ধন, কর্ণসুবর্ণ, সমতট ও তাম্রলিপ্তি এই পাঁচটি বিভিন্ন রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। উৎকল এবং কোঙ্গোদও তখন স্বাধীন রাজ্য ছিল। আৰ্য্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্পে উক্ত হইয়াছে যে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড়রাষ্ট্র আভ্যন্তরিক কলহ ও বিদ্রোহে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল; একাধিক রাজার অভ্যুদয় হয়-তাঁহার মধ্যে কেহ এক সপ্তাহ, কেহ বা এক মাস রাজত্ব করেন; শশাঙ্কের পুত্র মানব ৮ মাস ৫ দিন রাজত্ব করেন। এই বর্ণনা সম্ভবত অনেক পরিমাণে সত্য। এই প্রকার আত্মঘাতী অন্তর্বিদ্রোহই সম্ভবত শশাঙ্কের বিশাল রাজ্যের শক্তি নষ্ট এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণের পথ প্রশস্ত করে।
আঃ ৬৪১ অব্দে হর্ষবর্দ্ধন মগধ জয় করেন এবং পর বৎসর তিনি উত্তাল ও কোঙ্গোদে বিজয়াভিযান করেন। এই সময়েই কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মা গৌড় জয় করিয়া কর্ণসুবর্ণে তাঁহার জয়স্কন্ধাবার সন্নিবেশিত করেন। আঃ ৬৪২ অব্দে যখন হর্ষ জঙ্গল রাজ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন তখন ভাস্করবর্ম্মা বিশ হাজার রণহস্তী লইয়া হর্ষের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার ত্রিশ হাজার রণপোতও গঙ্গা নদী দিয়া কজঙ্গলে গমন করে। এইরূপে শশাঙ্কের দুই প্রবল শত্রু তাঁহার রাজ্যের ধ্বংস সাধন করে।
৬৪৬ অথবা ৬৪৭ অব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হয়। ইহার পরই তাঁহার সাম্রাজ্য ধ্বংস হয় এবং তিব্বতরাজ কামরূপ ও পূর্ব্বভারতের কিয়দংশ অধিকার করেন। সুতরাং গৌড়ে ভাস্করবর্ম্মার অধিকার খুব বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ইহার পরেই জয়নাগ নামক একজন রাজা কর্ণসুবর্ণে রাজত্ব করেন। তাঁহার মহারাজাধিরাজ উপাধি হইতে অনুমান হয় যে তিনি বেশ শক্তিশালী রাজা ছিলেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্যের বিস্তৃতি অথবা তাঁহার সম্বন্ধে আর কোনো বিবরণ জানা যায় না।
শশাঙ্কের মৃত্যুর পরবর্ত্তী একশত বৎসর গৌড়ের ইতিহাসে এক অন্ধকারময় যুগ। এই যুগে অনেক বহিঃশত্রু এই রাজ্য আক্রমণ করে। অনেকে অনুমান করেন যে তিব্বতরাজ ও পরবর্ত্তী গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণ এই রাজ্য জয় করিয়াছিলেন-কিন্তু ইহার বিশ্বাসযোগ্য কোনো প্রমাণ নাই। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে শৈলবংশীয় একজন রাজা পুদেশ জয় করেন। ইহার অনতিকাল পরে কনৌজের রাজা যশোবৰ্ম্মা গৌড়রাজকে পরাভূত ও বধ করেন। কনৌজের রাজকবি বাকপতিরাজ এই ঘটনা উপলক্ষ করিয়া গৌড়বহো (গৌড় বধ) নামক প্রাকৃত ভাষায় এক কাব্য রচনা করেন। কিন্তু ইহার পরেই কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্যের হাতে যশোবর্ম্মার পরাজয় ঘটে এবং তাঁহার বিশাল রাজ্য ধ্বংস হয়। গৌড়রাজ ললিতাদিত্যের অধীনতা স্বীকার করেন। রাজতরঙ্গিণী নামক কাশ্মীরের ইতিহাসে গৌড় সম্বন্ধে যে একটি আখ্যান লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ললিতাদিত্য গৌড়রাজকে কাশ্মীরে আমন্ত্রণ করেন এবং বিষ্ণুমূর্ত্তি স্পর্শ করিয়া শপথ করেন যে কাশ্মীরে গেলে তাঁহার কোনো বিপদ ঘটিবে না। অথচ গৌড়রাজ কাশ্মীর যাওয়ার পরেই ললিতাদিত্য তাঁহাকে হত্যা করেন। এই ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ লইবার জন্য গৌড়রাজের কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর তীর্থযাত্রার ছলে কাশ্মীর গিয়া উক্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি ভাঙ্গিবার জন্য মন্দিরে প্রবেশ করে। ভুলক্রমে তাহারা অন্য একটি মূর্ত্তি ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে এবং ইতিমধ্যে কাশ্মীরের সৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে হত্যা করে। রাজতরঙ্গিণীর রচয়িতা ঐতিহাসিক কুতুণ এই বাঙ্গালী বীর অনুচরগণের প্রভুভক্তি ও আত্মোৎসর্গের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন যে উক্ত মন্দিরটি আজও শূন্য কিন্তু পৃথিবী গৌড়বীরগণের প্রশংসায় পূর্ণ। কুতুণ ললিতাদিত্যকে আদর্শ রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন কিন্তু তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে চন্দ্রের ন্যায় ললিতাদিত্যের নির্মল চরিত্রে দুইটি দুরপনেয় কলঙ্ক ছিল এবং গৌড়রাজের হত্যা তাঁহার অন্যতম। রাজকবির এই সমুদয় উক্তি হইতে উল্লিখিত গৌড়বীরগণের কাহিনী সত্য বলিয়াই অনুমিত হয়।
কহ্লণ লিখিয়াছেন যে ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় পিতামহের অনুকরণে দিগ্বিজয়ে বাহির হন। কিন্তু তাঁহার অনুপস্থিতিতে জৰ্জ্জ কাশ্মীর রাজ্য অধিকার করে এবং জয়াপীড়ের সৈন্যগণও তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। অতঃপর সমুদয় অনুচরগণকে বিদায় দিয়া একাকী ছদ্মবেশে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীতে উপস্থিত হন। এই প্রদেশ তখন জয়ন্ত নামক একজন সামন্ত রাজার অধীনে ছিল। জয়াপীড় জয়ন্তের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং গৌড়ের পাঁচজন রাজাকে পরাস্ত করিয়া জয়ন্তকে তাঁহাদের অধীশ্বর করেন। এই কাহিনী কত দূর সত্য বলা যায় না। তবে গৌড় যে তখন পাঁচ অথবা একাধিক খণ্ডাজ্যে বিভক্ত ছিল, ইহা সম্ভব বলিয়াই মনে হয়।
নেপালের লিচ্ছবিরাজ দ্বিতীয় জয়দেবের শিলালিপিতে গৌড়ের আর এক বহিঃশত্রুর উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৫৩ সংবতে (৭৪৮ অথবা ৭৫৯ খৃষ্টাব্দ) উৎকীর্ণ এই লিপিতে নেপালরাজের শ্বশুর ভগদত্তবংশীয় রাজা হর্ষ গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ ও কোশলের অধিপতিরূপে অভিহিত হইয়াছেন। ভগদত্তবংশীয় রাজগণ কামরূপে রাজত্ব করিতেন, সুতরাং অনেকেই অনুমান করেন যে কামরূপরাজ হর্ষ গৌড় জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু উড়িষ্যার করবংশীয় রাজগণও ভগদত্তবংশীয় বলিয়া দাবী করিতেন। সুতরাং অসম্ভব নহে যে হর্ষ করবংশীয় রাজা ছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র গৌড়াধিপ এই সম্মানসূচক পদবী হইতে কামরূপ বা উৎকলের কোনো রাজা গৌড়ে রাজত্ব করিতেন এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না-তবে সম্ভবত তিনি গৌড়ে বিজয়াভিযান করিয়া কিছু সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।
.
২. বঙ্গ
রাজ্য শশাঙ্কের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল কি না নিশ্চিত বলা যায় না। কিন্তু শশাঙ্কের মৃত্যুর পরই যে এখানে সমতট নামে স্বাধীন রাজ্য ছিল হুয়েন সাংয়ের বিবরণ হইতেই তাহা জানা যায়। হুয়েন সাং আরও বলেন যে সমতটে এক ব্রাহ্মণবংশ রাজত্ব করিতেন, এবং এই বংশীয় শীলভদ্র তাঁহার সময়ে নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন।
অতঃপর খড়গবংশের অভ্যুদয় হয়। খড়েগাদ্যম, তৎপুত্র জাতখড়গ ও তৎপুত্র দেবখড়গ এই তিনজন রাজা সম্ভবত সপ্তম শতাব্দীর শেষার্ধে রাজত্ব করেন। দেখড়েগর পুত্র রাজরাজ অথবা রাজরাজভটও সম্ভবত তাঁহার পরে রাজত্ব করেন। এই রাজগণ সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহাদের রাজ্য দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গে বিস্তৃত ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে তাঁহাদের রাজধানীর নাম ছিল কৰ্ম্মান্ত এবং ইহাই বর্ত্তমানে কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী বড়কামতা নামে পরিচিত। কিন্তু এই মত নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায় না।
চীনদেশীয় পরিব্রাজক সেংচি সপ্তম শতাব্দীর শেষে এদেশে আসেন। তিনি সমতটের রাজা রাজভটের বৌদ্ধধর্ম্মে বিশেষ অনুরাগের কথা লিখিয়াছেন। সম্ভবত এই রাজভট ও খড়গবংশীয় রাজরাজ অভিন্ন। দেখগের রাণী প্রভাবতী কর্ত্তৃক একটি ধাতুময়ী সৰ্ব্বাণী (দুর্গা) মূৰ্তি কুমিল্লার ১৪ মাইল দক্ষিণে দেউলবাড়ী গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে।
কেহ কেহ মনে করেন যে খড়গবংশীয়েরা অষ্টম অথবা নবম শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। খড়গবংশীয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধেও সঠিক কিছু জানা যায় না। নেপালে খড়ুক অথবা খর্ক নামে এক বংশ ছিল। তাহাদের রাজা ক্ষত্রিয় বলিয়া দাবী করিতেন। ষোড়শ শতাব্দীতে এই বংশের রাজা দ্রব্য সাহ গুখা জিলা দখল করেন এবং বর্ত্তমান গুর্খা রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন খড়গ বংশের সহিত এই বংশের কোনো সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব নহে। তবে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।
কনৌজের রাজা যশোবৰ্ম্মা গৌড়রাজকে বধ করার পর বঙ্গ জয় করেন। বাকপতির বর্ণনা হইতে অনুমিত হয় যে বঙ্গরাজ বেশ শক্তিশালী ছিলেন এবং তাঁহার বহু রণহস্তী ছিল। গৌড়বহো কাব্যে উক্ত হইয়াছে যে যশোবর্ম্মার নিকট বশ্যতা স্বীকারের সময় বঙ্গবাসীদের মুখ পাণ্ডুর বর্ণ ধারণ করিয়াছিল, কারণ তাহারা এরূপ কাৰ্য্যে অভ্যস্ত নহে। বিদেশী কবি কর্ত্তৃক বঙ্গের বীরত্ব ও স্বাধীনতা প্রীতির উল্লেখ সম্ভবত তাঁহার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল। যশোবর্ম্মার অধিকার খুব বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। গৌড়ের অপর দুই বহিঃশত্রু ললিতাদিত্য ও হর্ষের সহিত বঙ্গের কোনো সম্বন্ধ ছিল না।
যশোবর্ম্মা যে সময় বঙ্গ জয় করেন, সে সময়েও খড়গবংশীয়েরা রাজত্ব করিতেছিলেন কি না বলা কঠিন। কারণ ইহার কিছু পূৰ্ব্বে রাত উপাধিধারী এক রাজবংশ কুমিল্লা অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। এই বংশীয় জীবধারণ রাত ও তাঁহার পুত্র শ্রীধারণ রাত এই দুই রাজার সমতটেশ্বর উপাধি ছিল এবং শ্রীধারণের তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে সমতটাদি অনেক দেশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। শ্রীধারণের সামন্তসূচক উপাধি হইতে অনুমিত হয় যে আদিতে এই বংশের রাজগণ কোনো রাজার অধীন ছিলেন কিন্তু শেষে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজত্ব করিতেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে রাতবংশ খড়গবংশের সামন্ত ছিল। কিন্তু এই দুই বংশ মোটামুটি সমসাময়িক হইলেও এই সিদ্ধান্ত নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করা যায় না। শ্রীধারণের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে ক্ষীরোদা নদী পরিবেষ্টিত দেবপৰ্বত এই বংশের রাজধানী ছিল। দেবপর্বত খুব সম্ভবত কুমিল্লা নগরীর পশ্চিমে লালমাই-ময়নামতী পাহাড়ের দক্ষিণভাগে অবস্থিত ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ময়নামতী টিলার প্রায় সাড়ে তিন মাইল দক্ষিণে পাহাড়ের পূর্ব্ব উপকণ্ঠে “আনন্দ রাজার বাড়ী” নামে বর্ত্তমানকালে পরিচিত স্থানই ঐ দেবপৰ্ব্বতের ধ্বংসাবশেষ-কারণ ইহার নিকটবর্ত্তী খাতটি এখনো স্থানীয় লোকের নিকট ক্ষীর নদী বলিয়া পরিচিত।
এই সময়কার একখানি তাম্রশাসনে সামন্তরাজ লোকনাথের ও তাঁহার পূৰ্বপুরুষগণের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহারা ত্রিপুরা অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। লোকনাথ ও জীবধারণ রাত সমসাময়িক ছিলেন কিন্তু উভয়ের মধ্যে কী সম্বন্ধ ছিল, সঠিক নির্ণয় করা যায় না। কাহারও কাহারও মতে লোকনাথ জীবধারণের সামন্ত ছিলেন, কিন্তু প্রথমে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল। জীবধারণ বহু সৈন্য ক্ষয় করিয়াও লোকনাথকে পরজিত করিতে পারেন নাই। কিন্তু পরে অন্য এক যুদ্ধে লোকনাথ তাঁহাকে সাহায্য করায় সন্তুষ্ট হইয়া তিনি লোকনাথকে বিস্তৃত ভূখণ্ডসহ শ্রীপট্ট দান করেন। এই মতটি নিশ্চিত সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা যায় না।
উল্লিখিত বর্ণনা হইতে অনুমিত হয় যে শশাঙ্ক-হর্ষবর্দ্ধন-ভাস্করবর্ম্মার তিরোধানের পরে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে পূৰ্ব্ববঙ্গে অনেকগুলি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। তিব্বতীয় লামা তারনাথ সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতীয় বৌদ্ধধৰ্ম্মের যে ইতিহাস রচনা করেন, তাহাতে এই যুগের বাংলা দেশের অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সমুদয় কাহিনী একেবারে অমূলক না হইলেও অন্যবিধ প্রমাণ ব্যতিরেকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। তিনি চন্দ্রবংশীয় অনেক রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। এই বংশের শেষ দুই রাজা গোবিচন্দ্র ও ললিতচন্দ্র। এই দুই রাজার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে বলিতে হয় যে এই চন্দ্রবংশীয় রাজারাই খড়গ অথবা রাতবংশীয়দের নিকট হইতে বঙ্গ জয় করেন এবং সম্ভবত ললিতচন্দ্রই যশোবর্ম্মার হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। রাজা গোপীচন্দ্র ও তাঁহার মাতা ময়নামতী সম্বন্ধে বঙ্গদেশে বহু প্রবাদ, কাহিনী ও গীতিকাব্য প্রচলিত আছে। ইহার মর্ম এই যে গোপীচন্দ্র অদুনা ও পদুনা নামক দুই রাণীকে পরিত্যাগ করিয়া যৌবনে মাতার আদেশে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন এবং হাড়ি সিদ্ধা অথবা হাড়িপার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। অনেকে মনে করেন যে তারনাথ কথিত গোবিচন্দ্র ও এই গোপীচন্দ্র অভিন্ন। কিন্তু এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।
০৬. পালসাম্রাজ্য
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ –পালসাম্রাজ্য
১. গোপাল (আ ৭৫০-৭৭০)
শশাঙ্কের মৃত্যুর পর শতবর্ষব্যাপী অনৈক্য, আত্মকলহ ও বহিঃশত্রুর পুনঃপুন আক্রমণের ফলে বাংলার রাজতন্ত্র ধ্বংসপ্রায় হইয়াছিল। প্রায় সহস্র বৎসর পরে তিব্বতীয় বৌদ্ধ লামা তারনাথ এই যুগের বাংলার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে সমগ্র দেশের কোনো রাজা ছিল না, প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, সম্ভ্রান্ত লোক, ব্রাহ্মণ, এবং বণিক নিজ নিজ এলাকা স্বাধীনভাবে শাসন করিতেন। ফলে লোকের দুঃখ-দুর্দশার আর সীমা ছিল না। সংস্কৃতে এইরূপ অরাজকতার নাম মাৎস্যন্যায়। পুকুরের যেমন বড় মাছ ছোট মাছ খাইয়া প্রাণ ধারণ করে, দেশে অরাজকতার সময় সেইরূপ প্রবল অবাধে দুৰ্ব্বলের উপর অত্যাচার করে, এই জন্যই মাৎস্যন্যায় এই সংজ্ঞার উৎপত্তি। সমসাময়িক লিপিতে বাংলা দেশে মাৎস্যন্যায়ের উল্লেখ আছে-সুতরাং তারনাথের বর্ণনা মোটামুটি সত্য বলিয়াই গ্রহণ করা যায়। এই চরম দুঃখ-দুর্দশা হইতে মুক্তিলাভের জন্য বাঙ্গালী জাতি যে রাজনৈতিক বিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা ও আত্মত্যাগের পরিচয় দিয়াছিল, ইতিহাসে তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। দেশের প্রবীণ নেতাগণ স্থির করিলেন যে পরস্পর বিবাদ-বিসংবাদ ভুলিয়া একজনকে রাজপদে নির্বাচিত করিবেন এবং সকলেই স্বেচ্ছায় তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিবেন। দেশের জনসাধারণও সানন্দে এই মত গ্রহণ করিল। ইহার ফলে গোপাল নামক এক ব্যক্তি বাংলা দেশের রাজপদে নিৰ্বাচিত হইলেন। এইরূপে কেবলমাত্র দেশের মঙ্গলের দিকে চাহিয়া ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জনপূর্ব্বক সর্ব্বসাধারণে মিলিয়া কোনো বৃহৎ কাৰ্য্য অনুষ্ঠান যেমন বাঙ্গালীর ইতিহাসে আর দেখা যায় না, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে এই মহান স্বার্থত্যাগ ও ঐক্যের ফলে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন যে উন্নতি ও গৌরবের চরম শিখরে উঠিয়াছিল, তাঁহার দৃষ্টান্তও বাংলার ইতিহাসে আর নাই। ১৮৬৭ অব্দে জাপানে যে গুরুতর রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, কাৰ্য্য, কারণ ও পরিণাম বিবেচনা করিলে তাঁহার সহিত সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে গোপালের রাজপদে নির্বাচনের তুলনা করা যাইতে পারে।
গোপালের বংশপরিচয় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। গোপাল ও তাঁহার বংশধরগণ সকলেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। পালরাজগণের তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে গোপালের পিতামহ দয়িতবিষ্ণু সর্ব্ববিদ্যাবিশুদ্ধ ছিলেন এবং গোপালের পিতা বপট শক্রর দমন এবং বিপুল কীর্তিকলাপে সসাগরা বসুন্ধরাকে ভূষিত করিয়াছিলেন। সুতরাং গোপাল যে কোনো রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এরূপ মনে হয় না। তাঁহার পিতা যুদ্ধ ব্যবসায়ী ছিলেন এবং গোপালও সম্ভবত পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া প্রবীণ ও সুনিপুণ যোদ্ধা বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। কারণ এই সঙ্কট সময়ে বাংলার নেতাগণ যে বংশমর্যাদাহীন যুদ্ধানভিজ্ঞ তরুণ-বয়স্ক কোনো ব্যক্তিকে রাজপদে নির্বাচন করিয়াছিলেন, এরূপ সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। পরবর্ত্তীকালে পালগণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন। গোপালের পুত্র ধর্ম্মপাল সমসাময়িক একখানি গ্রন্থে ‘রাজভটাদিবংশ পতিত’ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে পালরাজগণ খড়গবংশীয় রাজা রাজরাজভটের বংশধর। কিন্তু এখানে রাজভট শব্দ রাজসৈনিক অর্থে গ্রহণ করাই অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে হয়। ইহা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থক।
গোপালের তারিখ সঠিক জানা যায় না। তবে তিনি অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজপদে নিৰ্বাচিত হইয়াছিলেন, ইহাই সম্ভবপর মনে হয়। প্রায় চারিশত বর্ষ পরে রচিত রামচরিত গ্রন্থে বরেন্দ্রভূমি পালরাজগণের ‘জনকভূ’ অর্থাৎ পিতৃভূমি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে গোপাল বরেন্দ্রের অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রথমেই সমগ্র বাংলা দেশের অধিপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন কি না তাহা সঠিক জানা যায় না। কিন্তু তাঁহার রাজ্যকালে সমগ্র বঙ্গদেশই তাঁহার শাসনাধীন হইয়াছিল এবং বহুদিন পরে বাংলায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির সহিত সুখ ও শান্তি ফিরিয়ে আসিয়াছিল। ইহাই গোপালের প্রধান কীর্তি। তাঁহার রাজ্যকালের কোনো বিবরণই আমরা জানি না। কিন্তু তিনি যে শতাব্দীব্যাপী বিশৃঙ্খলার পর তাঁহার রাজ্য এমন শক্তশালী ও সুসমৃদ্ধ করিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র যে সমগ্ৰ আৰ্য্যাবর্তে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহার রাজোচিত গুণাবলী ও ভূয়োদর্শনের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।
.
২. ধর্ম্মপাল (আ ৭৭০-৮১০)
গোপালের মৃত্যুর পর আ ৭৭০ অব্দে তাঁহার পুত্ৰ ধৰ্ম্মপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। ধর্ম্মপাল বীর, সাহসী ও রাজনীতিকুশল ছিলেন। গোপালের সুশাসনের ফলে বাংলা দেশের শক্তি ও সমৃদ্ধি অনেক বাড়িয়েছিল। সুতরাং ধর্ম্মপাল প্রথম হইতেই আৰ্য্যাবৰ্ত্তে এক সাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পনায় মাতিয়া উঠিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার এক প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত হইল। ইনি প্রতীহারবংশীয় রাজা বৎসরাজ। প্রতীহারেরা সম্ভবত গুজ্জরজাতীয় ছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই গুজ্জর জাতি হূণদিগের সঙ্গে বা অব্যবহিত পরে ভারতে আসিয়া পাঞ্জাব রাজপুতানা ও মালবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করে। অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধে মালব ও রাজপুতানার প্রতীহার রাজা বৎসরাজ বিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠেন। যে সময় ধর্ম্মপাল বাংলা দেশ হইতে পশ্চিম দিকে বিজয়াভিযান করেন, সেই সময় বসরাজও সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টায় পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হন। ফলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হয় এবং ধর্ম্মপাল পরাজিত হন। কিন্তু ধর্ম্মপালের সৌভাগ্যক্রমে এই সময় দক্ষিণাপথের রাষ্ট্রকুটরাজ ধ্রুব আৰ্য্যাবর্তে বিজয়াভিযান করিয়া বসরাজকে পরাজিত করেন। বসরাজ পলাইয়া মরুভূমিতে আশ্রয় লইলেন এবং তাঁহার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আশা দূরীভূত হইল।
ধ্রুব বৎসরাজকে পরাস্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি ধর্ম্মপালের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ধর্ম্মপাল ইতিমধ্যে মগধ, বারাণসী, ও প্রয়াগ জয় করিয়া গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। এইখানেই ধ্রুবের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল। রাষ্ট্রকূটরাজের প্রশস্তিমতে ধ্রুব ধৰ্ম্মপালকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে ধর্ম্মপালের বিশেষ কোনো অনিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ধ্রুব শীঘ্রই দক্ষিণাপথে ফিরিয়া গেলেন। এবং ধর্ম্মপালের আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না। এই সুযোগে ধর্ম্মপাল ক্রমে ক্রমে প্রায় সমগ্ৰ আৰ্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়া নিজের আধিপত্য স্থাপন করিলেন। ইহার ফলে তিনি সার্বভৌম সম্রাটের পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং গৌরবসূচক ‘পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ’ প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করিলেন।
ধর্ম্মপালের পুত্র দেবপালের তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে ধৰ্ম্মপাল দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া কেদার ও গোকর্ণ এই দুই তীর্থ এবং গঙ্গাসাগর সঙ্গম দর্শন করিয়াছিলেন। কেদার হিমালয়ে অবস্থিত সুপরিচিত তীর্থ। গোকর্ণের অবস্থিতি লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কাহারও মতে ইহা বোম্বে প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত উত্তর কাণাড়ায় অবস্থিত সুপরিচিত গোকর্ণ নামক তীর্থ। কিন্তু ধর্ম্মপাল যে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটরাজ্য পার হইয়া এই দূরদেশে বিজয়াভিযান করিয়াছিলেন বিশিষ্ট প্রমাণ অভাবে তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। নেপালে বাগমতী নদীর তীরে পশুপতি মন্দিরের দুই মাইল উত্তর-পূর্ব্বে গোকর্ণ নামে তীর্থ আছে–সম্ভবত ধর্ম্মপাল এই স্থানে গমন করিয়াছিলেন। এই অনুমানের সপক্ষে বলা যাইতে পারে যে স্বয়ম্ভুপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে গৌড়রাজ ধর্ম্মপাল নেপালের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। গোকর্ণ যেখানেই অবস্থিত হউক, ধৰ্ম্মপালের সেনাবাহিনী দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া যে পাঞ্জাবের প্রান্ত পর্য্যন্ত বিজয়াভিযান করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।
আর্য্যাবর্তে আধিপত্য লাভ করিবার জন্য ধর্ম্মপালকে বহু যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু উক্ত দিগ্বিজয়ের উল্লেখ ব্যতীত পালরাজগণের প্রশস্তিতে এই সমুদয় যুদ্ধের বিশদ কোনো বিবরণ নাই। এই দিগ্বিজয়ের প্রারম্ভেই তিনি ইন্দ্ররাজ প্রভৃতিকে জয় করিয়া মহোদয় অর্থাৎ কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছিলেন। প্রাচীন পাটলিপুত্র ও বর্ত্তমান দিল্লীর ন্যায় তৎকালে কান্যকুব্জই আৰ্য্যাবর্তের রাজধানী বলিয়া বিবেচিত হইত, এবং সাম্রাজ্য স্থাপনে অভিলাষী রাজগণ কান্যকুজের দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন। ধর্ম্মপাল কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া ক্রমে সিন্ধু নদ ও পাঞ্জাবের উত্তরে হিমালয়ের পাদভূমি পৰ্য্যন্ত জয় করিলেন। দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করিয়াও তিনি সম্ভবত কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। এইরূপে আর্য্যাবর্তের সার্বভৌমত্ব লাভ করিয়া ইহা প্রকাশ্যে ঘোষণা করিবার জন্য তিনি কান্যকুজে এক বৃহৎ রাজাভিষেকের আয়োজন করিলেন। এই রাজদরবারে আর্য্যাবর্তের বহু সামন্ত নরপতিগণ উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মপালের অধিরাজত্ব স্বীকার করিলেন। মালদহের নিকটবর্ত্তী খালিমপুরে প্রাপ্ত ধৰ্ম্মপালের তাম্রশাসনে এই ঘটনাটি নিম্নলিখিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। “তিনি মনোহর ভঙ্গি-বিকাশে ইঙ্গিত মাত্রে] ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গন্ধার এবং কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের [সামন্ত?] নরপালগণকে প্রণতিপরায়ণ চঞ্চলাবনত মস্তকে সাধু সাধু বলিয়া কীৰ্ত্তন করাইতে করাইতে হৃদচিত্ত পাঞ্চালবৃদ্ধকর্ত্তৃক মস্তকোপরি আত্মাভিষেকের স্বর্ণকলস উদ্ধৃত করাইয়া কান্যকুব্জকে রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলন।”
এই শ্লোকে যে সকল রাজ্যের উল্লেখ আছে, তাহাদের রাজগণ সকলেই কান্যকুজে আসিয়াছিলেন এবং যখন পঞ্চাল দেশের বয়োবৃদ্ধগণ ধর্ম্মপালের মস্ত কে স্বর্ণকলস হইতে পবিত্র তীর্থজল ঢালিয়া তাঁহাকে কান্যকুজের রাজপদে অভিষেক করিতেছিলেন তখন নতশিরে ‘সাধু সাধু’ বলিয়া এই কাৰ্য্য অনুমোদন করিয়াছিলেন-অর্থাৎ তাঁহাকে রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়াছিলেন। সুতরাং অন্তত ঐ সমুদয় রাজ্যই যে ধৰ্ম্মপালের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। ইহার মধ্যে গন্ধার, মদ্র, কুরু ও কীর দেশ যথাক্রমে পঞ্চনদের পশ্চিম, মধ্য, পূর্ব্ব ও উত্তর ভাগে অবস্থিত। যবন দেশ সম্ভবত সিন্ধু নদের তীরবর্ত্তী কোনো মুসলমান অধিকৃত রাজ্য সূচিত করিতেছে। অবন্তি মালবের এবং মৎস্যদেশ আলওয়ার ও জয়পুর রাজ্যের প্রাচীন নাম। ভোজ ও যদু একাধিক রাজ্যের নাম ছিল। সুতরাং ইহা দ্বারা ঠিক কোন কোন দেশ সূচিত হইয়াছে, তাহা বলা কঠিন। সম্ভবত ভোজরাজ্য বর্ত্তমান বেরারে এবং যদুরাজ্য পাঞ্জাবে অথবা সুরাষ্ট্রে অবস্থিত ছিল।
এই সমুদয় রাজ্যের অবস্থিতি আলোচনা করিলে সহজেই অনুমিত হইবে যে ধর্ম্মপাল প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্তের অধীশ্বর ছিলেন। পালরাজগণের প্রশস্তি ব্যতীত অন্যত্রও ধর্ম্মপালের এই সাৰ্বভৌমত্বের উল্লেখ আছে। একাদশ শতাব্দীতে রচিত সোড়ল প্রণীত উদয়সুন্দরীকথা নামক চম্পু-কাব্যে ধর্ম্মপাল উত্তরাপথস্বামী বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।
এই বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে মাত্র বাংলা দেশ ও বিহার ধর্ম্মপালের নিজ শাসনাধীনে ছিল। অন্যান্য পরাজিত রাজগণ ধর্ম্মপালের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া স্বীয় স্বীয় রাজ্য শাসন করিতেন। কেবলমাত্র কান্যকুজে পরাজিত ইন্দ্ররাজের পরিবর্তে ধর্ম্মপাল চক্ৰায়ুধ নামক একজন নূতন ব্যক্তিকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।
ধর্ম্মপাল নিরুদ্বেগে এই বিশাল সাম্রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার পূর্ধ্বতন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতীহাররাজ বৎসরাজের পুত্র নাগভট শীঘ্রই কতক রাজ্য জয় এবং কতক রাজ্যের সহিত মিত্ৰতা স্থাপনপূৰ্ব্বক স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করিয়া ধৰ্ম্মপালের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তিনি প্রথমে চক্ৰায়ুধকে পরাজিত করেন, এবং চক্ৰায়ুধ ধৰ্ম্মপালের শরণাপন্ন হন। অবশেষে ধৰ্ম্মপালের সহিত নাগভটের বিষম যুদ্ধ হয়। প্রতীহাররাজের প্রশস্তি অনুসারে নাগভট এই যুদ্ধে জয়ী হন। কিন্তু অচিরকাল মধ্যেই রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ নাটভটের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেন এবং বৎসরাজের ন্যায় নাগভট্টের সাম্রাজ্য স্থাপনের আশাও দূরীভূত হয়।
রাষ্ট্রকূটরাজগণের প্রশস্তি অনুসারে ধর্ম্মপাল ও চক্ৰায়ুধ উভয়ে স্বেচ্ছায় তৃতীয় গোবিন্দের আনুগত্য স্বীকার করেন। ইহা হইতে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে ধৰ্ম্মপাল ও চক্ৰায়ুধ নাগভটকে দমন করিবার নিমিত্তই রাষ্ট্রকূটরাজের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের আমন্ত্রণেই তৃতীয় গোবিন্দ নাটভাটের রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন। সে যাহাই হইক, পিতার ন্যায় তৃতীয় গোবিন্দও শীঘ্রই দক্ষিণাপথে রহিল না। নাগভট্টের পরাজয় এরূপ গুরুতর হইয়াছিল যে, তিনি এবং তাঁহার পুত্র আর পালরাজগণের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে পারিলেন না। সুতরাং ধর্ম্মপালের বিশাল সাম্রাজ্য অটুট রহিল এবং সম্ভবত শেষ বয়সে তিনি শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন।
ধর্ম্মপালের বাহুবলে বাংলা দেশে যেরূপ গুরুতর রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল সচরাচর তাঁহার দৃষ্টান্ত মিলে না। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে যে দেশ পরপদানত এবং অরাজকতা ও অত্যাচারের লীলাভূমি ছিল সেই দেশ সহসা প্রচণ্ড শক্তিশালী হইয়া সমগ্র আর্য্যাবর্তে নিজের প্রভুত্ব বিস্তার করিবে ইহা অলৌকিক কাহিনীর মতোই অদ্ভুত মনে হয়। এই সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালীর নূতন জাতীয় জীবনের সূত্রপাত হয়। ধৰ্ম্ম শিল্প ও সাহিত্যের অভ্যুদয়েই এই জাতীয় জীবন প্রধানত আত্মবিকাশ করিয়াছিল। পালরাজগণের চারিশত বর্ষব্যাপী রাজ্যকাল বাঙ্গালী জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগ। ধর্ম্মপালের রাজ্য বাঙ্গালীর জীবন প্রভাত।
এই নূতন যুগের বাঙ্গালীর আশা-আকাক্ষা কল্পনা ও আদর্শ সমসাময়িক রচনার মধ্য দিয়া কিয়ৎ পরিমাণে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। খালিমপুর তাম্রশাসনে ধর্ম্মপালের ‘পাটলিপুত্ৰনগর-সমাবাসিত-শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারের’ যে বর্ণনা আছে, তাহাতে নবসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার গর্বে দৃপ্ত বাঙ্গালীর মানচিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। অশোকের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত মৌৰ্য্য রাজগণের প্রাচীন রাজধানী পাটলিপুত্রে (বর্ত্তমান পাটনা) ধর্ম্মপাল সাময়িক অথবা স্থায়ীভাবে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। কবি তাঁহার বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে এখানে গঙ্গাবক্ষে অসংখ্য বিশাল রণতরীর সমাবেশ সেতুবন্ধ রামেশ্বরের শৈলশিখরশ্রেণী বলিয়া মনে হইত; এখানকার অসংখ্য রণহস্তী দিনশোভাকে স্নান করিয়া নিবিড় মেঘের শোভা সৃষ্টি করিত; উত্তরাপথের বহু সামন্তরাজগণ যে অগণিত অশ্ব উপঢৌকনস্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন তাহাদের ক্ষুরোখিত ধূলিজালে এই স্থান চতুর্দিক ধূসরিত হইয়া থাকিত; এবং রাজরাজেশ্বর ধর্ম্মপালের সেবার জন্য সমস্ত জম্বুদ্বীপ (ভারতবর্ষ) হইতে যে সমস্ত রাজগণ এখানে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের অনন্ত পদাতিসেনার পদভারে বসুন্ধরা অবনত হইয়া থাকিত। শক্তি, সম্পদ ও ঐশ্বর্য্যের এই বর্ণনার মধ্যে যে আতিশয্য আছে তাহা বাঙ্গালীর তল্কালীন জাতীয় মনোভাবের পরিচায়ক।
এই নূতন জাতীয় জীবনের সৃষ্টিকর্ত্তা ধর্ম্মপালকে বাঙ্গালী কী চক্ষে দেখিত তাহা অনায়াসেই আমরা কল্পনা করিতে পারি। কবি একটিমাত্র শ্লোকে তাঁহার একটু আভাস দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে সীমান্তদেশে গোপগণ, বনে বনচরগণ, গ্রামসমীপে জনসাধারণ, প্রত্যেক গৃহপ্রাঙ্গণে ক্রীড়ারত শিশুগণ, প্রতি দোকানে ক্রয়বিক্রয়কারীগণ, এমনকি বিলাসগৃহের পিঞ্জরস্থিত শুকগণও সৰ্ব্বদা ধর্ম্মপালের গুণগান করিত; সুতরাং ধর্ম্মপাল সৰ্ব্বত্র এই আত্মম্ভতি শ্রবণ করিতেন এবং লজ্জায় সৰ্ব্বদাই তাঁহার বদনমণ্ডল নত হইয়া থাকিত।
একদিন বাংলার মাঠে-ঘাটে ঘরে-বাহিরে যাহার নাম লোকের মুখে মুখে ফিরিত, তাঁহার কোনো স্মৃতিই আজ বাংলা দেশে নাই। অদৃষ্টের নিদারুণ পরিহাসে বাঙ্গালী তাঁহার নাম পৰ্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিল। কয়েকখানি তাম্রশাসন ও শিলালিপি এবং তিব্বতীয় গ্রন্থের সাহায্যে আমরা তাঁহার কীর্তিকলাপের ক্ষীণ প্রতিধ্বনিমাত্র পাইয়াছি, কিন্তু তাঁহার জীবনীর বিশেষ কোনো বিবরণ জানিতে পারি নাই। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য, বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য যে কয়েকটি স্কুল ঘটনা ব্যতীত এই মহাবীর ও মহাপুরুষের ব্যক্তিগত জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে আর কিছুই জানিবার উপায় নাই।
ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূটরাজ পরবলের কন্যা রন্নাদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই পরবল কে এবং কোথায় রাজত্ব করিতেন, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছুই বলা যায় না। ৮৬১ অব্দে উত্তীর্ণ রাষ্ট্রকূটবংশীয় পরবল নামক রাজার একখানি শিলালিপি মধ্যভারতে পাওয়া গিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে ইনিই রন্নাদেবীর পিতা। কিন্তু ঐ তারিখের অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেই দীর্ঘকাল রাজত্বের পর ধর্ম্মপালের মৃত্যু হয়। সুতরাং একেবারে সম্ভব না হইলেও ধর্ম্মপালের সহিত উক্ত পরবলের কন্যার বিবাহ খুব অস্বাভাবিক ঘটনা বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। রন্নাদেবী দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রকূটবংশের কোনো রাজকন্যা ছিলেন এই মতটিই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয়।
ধর্ম্মপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাপাল অনেক যুদ্ধে তাঁহার সেনাপতি ছিলেন এবং গর্গ নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। বাপাল ও গর্গের বংশধরগণের লিপিতে এই দুইজনের কৃতিত্ব বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং প্রধানত তাঁহাদের সাহায্যেই যে ধর্ম্মপালসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় সফলকাম হইয়াছিলেন এরূপ স্পষ্ট ইঙ্গিতও আছে। এই উক্তির মধ্যে কিছু সত্য থাকিলেও ইহা যে অতিরঞ্জন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।
পিতার ন্যায় ধর্ম্মপালও বৌদ্ধ ছিলেন। তিব্বতদেশীয় গ্রন্থে ধর্ম্মপালের অনেক কীর্তিকলাপের উল্লেখ আছে। মগদে তিনি একটি বিহার বা বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করেন। তাঁহার বিক্রমশীল এই দ্বিতীয় নাম বা উপাধি অনুসারে ইহা ‘বিক্রমশীলবিহার’ নামে অভিহিত হয়। নালন্দার ন্যায় বিক্রমশীল বিহারও ভারতের সৰ্ব্বত্র ও ভারতের বাহিরে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। গঙ্গাতটে এক শৈলশিখরে অবস্থিত এই বিহারে একটি প্রধান মন্দির এবং তাঁহার চারিদিকে ১০৭টি ছোট মন্দির ছিল। এটি একটি উচ্চ শিক্ষাকেন্দ্র ছিল এবং ১১৪ জন শিক্ষক এখানে নানা বিষয় অধ্যাপনা করিতেন। তিব্বতের বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু এখানে অধ্যয়ন করিতে আসিতেন এবং এখানকার অনেক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ আচাৰ্য্য তিব্বতে বিশুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। বরেন্দ্র ভূমিতে সোমপুর নামক স্থানে ধৰ্ম্মপাল আর একটি বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। রাজসাহী জিলার অন্তর্গত পাহাড়পুর নামক স্থানে ইহার বিরাট ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এত বড় বৌদ্ধবিহার ভারতবর্ষের আর কোথাও ছিল বলিয়া জানা যায় নাই। যে সুবিস্তৃত অঙ্গনের চতুর্দিক ঘিরিয়া এই বিহারটি ছিল, তাঁহার মধ্যস্থলে এক বিশাল মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এই প্রকার গঠনরীতি ভারতবর্ষের আর কোনো মন্দিরে দেখা যায় না। শিল্প-শীর্ষক অধ্যায়ে এই মন্দির ও বিহারের বর্ণনা করা যাইবে। পাহাড়পুরের নিকটবর্ত্তী ওমপুর গ্রাম এখনো প্রাচীন সোমপুরের স্মৃতি রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ওদন্ত পুরেও (বিহার) ধর্ম্মপাল সম্ভবত একটি বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় লেখক তারনাথের মতে ধৰ্ম্মপাল ধৰ্ম্মশিক্ষার জন্য ৫০টি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।
ধর্ম্মপাল নিজে বৌদ্ধ হইলেও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তাঁহার কোনো বিদ্বেষ ছিল না। নারায়ণের এক মন্দিরের জন্য তিনি নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। তিনি শাস্ত্রানুশাসন মানিয়া চলিতেন এবং প্রতি বর্ণের লোক যাহাতে স্বধর্ম্ম প্রতিপালন করে তাঁহার ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ এবং ইঁহার বংশধররা বহুপুরুষ পৰ্য্যন্ত বৌদ্ধ পালরাজগণের প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেকালে যে রাজার ব্যক্তিগত ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত রাজ্যশাসন ব্যাপারের কোনো সম্বন্ধ ছিল না এই দৃষ্টান্ত হইতে তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।
খালিমপুর তাম্রশাসন ধৰ্ম্মপালের বিজয়রাজ্যের ৩২ সম্বৎসরে লিখিত। ইহার পর ধর্ম্মপাল আর কত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। তারনাথের মতে ধর্ম্মপালের রাজ্যকাল ৬৪ বৎসর-কিন্তু ইহার সমর্থক কোনো প্রমাণ নাই।
ধর্ম্মপালের মৃত্যুর পর রন্নাদেবীর গর্ভজাত তাঁহার পুত্র দেবপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। ধর্ম্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসনে কিন্তু যুবরাজ ত্রিভুবন পালের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই যুবরাজ ত্রিভুবনপালই দেবপাল নামে রাজা হন অথবা জ্যেষ্ঠভ্রাতা ত্রিভুবনপালের মৃত্যুতে কনিষ্ঠ দেবপাল পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। এই শেষোক্ত অনুমানই সত্য বলিয়া মনে হয়। কারণ খালিমপুর তাম্রশাসনে রাজপুত্র দেবটেরও উল্লেখ আছে এবং অসম্ভব নহে যে ইহা দেবপাল নামের অপভ্রংশ। অবশ্য ত্রিভুবনপাল জীবিত থাকিলেও কনিষ্ঠ দেবপাল সিংহাসন অধিকার করিয়া থাকিতে পারেন। কিন্তু এ সকলই অনুমান মাত্র।
.
৩. দেবপাল (আ ৮১০-৮৫০)
পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ দেবপাল পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন এবং পিতৃসাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি অনেক যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন এবং নূতন নূতন রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে তাঁহার বিজয়বাহিনী দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্বত ও পশ্চিমে কাম্বোজ দেশ অর্থাৎ কাশ্মীরের সীমান্ত পৰ্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। তাঁহার সেনাপতি ও মন্ত্রীগণের বংশধরদের লিপিতে বিজিত রাজ্যের তালিকা পাওয়া যায়। পিতৃব্য বাকপালের পুত্র জয়পাল তাঁহার সেনাপতি ছিলেন। জয়পালের বংশধর নারায়ণপালের তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে জয়পাল দিগ্বিজয়ে অগ্রসর হইলে উল্কলের রাজা দূর হইতে তাঁহার নামমাত্র শ্রবণ করিয়াই অবসন্ন হইয়া নিজের রাজধানী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রাগজ্যোতিষের (আসাম) রাজা জয়পালের আজ্ঞায় যুদ্ধোদ্যম ত্যাগ করিয়া পালরাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালের মন্ত্রী গর্গের পুত্র দর্ভপাণি এবং প্রপৌত্র কেদারমিশ্র উভয়েই দেবপালের রাজ্যকালে প্রধানমন্ত্রীর পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। কেদারমিশ্রের পুত্র গুরবমিশ্রের লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে দর্ভপাণির নীতিকৌশলে দেবপাল হিমালয় হইতে বিন্ধ্যপর্বত এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী সমগ্র ভূভাগ করপ্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই লিপিতে আরও উক্ত হইয়াছে যে মন্ত্রী কেদারমিশ্রের বুদ্ধিবলের উপাসনা করিয়া গৌড়েশ্বর দেবপালদেব উৎকলকুল ধ্বংস, হূণগৰ্ব খৰ্ব্ব এবং দ্রবিড় ও গুজ্জরনাথের দর্প চূর্ণ করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত আসমুদ্র পৃথিবী উপভোগ করিয়াছিলেন।
উল্লিখিত লিপি দুইখানির মতে দেবপালের রাজত্বের যত কিছু গৌরব ও কৃতিত্ব তাহা কেবল মন্ত্রীদ্বয় ও সেনাপতিরই প্রাপ্য। গুরবমিশ্রের লিপিতে ইহাও বলা হইয়াছে যে অগণিত রাজন্যবর্গের প্রভু সম্রাট দেবপাল (উপদেশ গ্রহণের জন্য স্বয়ং) দৰ্ভপাণির অবসরের অপেক্ষায় তাঁহার দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া থাকিতেন এবং রাজসভার আগে এই মন্ত্রীবরকে মূল্যবান আসন দিয়া নিজে ভয়ে ভয়ে সিংহাসনে বসিতেন।
যখন এই সমুদয় উক্তি লিখিত হয় তখন পালবংশের বড়ই দুর্দিন। সুতরাং তখনকার হতমান দুৰ্বলচিত্ত পালরাজের পক্ষে এই প্রকার আচরণ সম্ভবপর হইলেও ধর্ম্মপালের পুত্র আর্য্যাবর্তের অধীশ্বর দেবপালদেবের সম্বন্ধে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। এই সমুদয় অত্যুক্তির মধ্যে কী পরিমাণ সত্য নিহিত আছে তাঁহার অনুসন্ধান নিষ্প্রয়োজন। কারণ দেবপালের রাজ্যকাল বাংলার সাম্রাজ্য বিস্তারই ইতিহাসের মুখ্য ঘটনা, তাহা কী পরিমাণে সেনাপতির বাহুবলে অথবা মন্ত্রীর বুদ্ধিকৌশলে হইয়াছিল এই বিচার অপেক্ষাকৃত গৌণ বিষয়।
উপরে বিজিত রাজগণের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, দেবপাল উড়িষ্যা ও আসাম বাংলার এই দুই সীমান্ত প্রদেশ জয় করেন। আসামের রাজা বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করিয়া সামন্ত রাজার ন্যায় রাজত্ব করিতেন। কিন্তু উড়িষ্যার রাজাকে দূরীভূত করিয়া উড়িষ্যা সম্ভবত পালরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। উকলাধীশের রাজধানী পরিত্যাগ এবং ‘উকীলিতোকলকুল’ এই প্রকার পদপ্রয়োগ এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করে। উড়িষ্যার ভঞ্জ রাজবংশের লিপি হইতে জানা যায় যে, রণভঞ্জের পর এই বংশীয় রাজগণ প্রাচীন খিঞ্জলী রাজ্য ও রাজধানী ত্যাগ করিয়া উড়িষ্যার দক্ষিণ সীমান্তে গঞ্জাম জিলায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রণভঞ্জ সম্ভবত নবম শতাব্দের প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং খুব সম্ভব যে এই বংশীয় রাজাকে দূর করিয়াই দেবপাল উড়িষ্যা, অন্তত তাঁহার অধিকাংশ ভাগ, অধিকার করেন।
দেবপাল যে হৃণজাতির গৰ্ব্ব খৰ্ব্ব করেন তাহাদের রাজ্য কোথায় ছিল তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে হূণজাতি আৰ্য্যাবৰ্ত্তের পশ্চিম ভাগে বিস্তৃত রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা ক্রমশ হীনবল হইয়া পড়ে এবং বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করে। হর্ষচরিত পাঠে জানা যায় যে, উত্তরাপথে হিমালয়ে নিকটে হূণদের একটি রাজ্য ছিল। সম্ভবত দেবপাল এই রাজ্য জয় করিয়া কাম্বোজ পৰ্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। কাম্বোজ পঞ্চনদের উত্তর পশ্চিমে ও গন্ধারের ঠিক উত্তরে এবং হূণরাজ্যের ন্যায় পালসাম্রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত ছিল। সুতরাং এই দুই রাজ্যের সহিত দেবপালের বিরোধ খুবই স্বাভাবিক। এখানে বলা আবশ্যক যে মালব প্রদেশেও একটি হূণরাজ্য ছিল।
দেবপাল যে গুজ্জর রাজার দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন তিনি সম্ভবত নাগভট্টের পৌত্র প্রথম ভোজ। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের হস্তে নিদারুণ পরাজয়ের পর প্রতীহাররাজ নাগভট ও তাঁহার পুত্র রামভদ্রের শক্তি অতিশয় ক্ষীণ হইয়াছিল। রামভদ্রের রাজ্যকালে প্রতীহার রাজ্য শত্রু কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল এরূপ ইঙ্গিতও এই বংশের লিপিতে পাওয়া যায়। তৎপুত্র ভোজ প্রথমে কিছু সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, কারণ তিনি ৮৩৬ অব্দে কনৌজ ও কালঞ্জরের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ৮৬৭ অব্দের পূর্ব্বে রাষ্ট্রকূটরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত এবং ৮৬৯ অব্দের পূর্ব্বে স্বীয় রাজ্য গুজ্জরা (বর্ত্তমান রাজপুতনা) হইতে বিতাড়িত হন। সম্ভবত ৮৪০ হইতে ৮৬০ অব্দের মধ্যে দেবপাল তাঁহাকে পরাজিত করেন।
এইরূপে দেখিতে পাই যে, ধর্ম্মপাল যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন দেবপাল তাঁহার সীমান্তস্থিত কামরূপ, উল্কল, হূণদেশ ও কামোজ জয় করেন এবং চিরশত্রু প্রতীহাররাজকে পরাজিত করেন। সুতরাং প্রশস্তিকার যে তাঁহার রাজ্য হিমালয় হইতে বিন্ধ্যপর্বত এবং পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন তাহা মোটামুটিভাবে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়।
মুঙ্গেরে প্রাপ্ত দেবপালের তাম্রশাসনে তাঁহার সাম্রাজ্য হিমালয় হইতে রামেশ্বর সেতুবন্ধ পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহা অতিরঞ্জিত এবং নিছক কবিকল্পনা বলিয়াই সকলে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার মূলে কিছু সত্য থাকিতে পারে। দেবপাল যে দ্রবিড়নাথের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটরাজ বলিয়াই গ্রহ করিয়াছেন। প্রতীহার রাজার ন্যায় রাষ্ট্রকূট রাজার সহিতও পালরাজগণের বংশানুক্রমিক শত্রুতা ছিল, সুতরাং দেবপাল কোনো রাষ্ট্রকূটরাজাকে পরাভূত করিয়া থাকিবেন ইহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু দ্রবিড় বলিতে সাধারণত দাক্ষিণাত্য বুঝায় না, ইহা দক্ষিণ ভারত অর্থাৎ কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণস্থিত ভূভাগের নাম। এই সুদূর দেশে যে দেবপাল যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন ইহার সপক্ষে কোনো প্রমাণ না থাকাতেই পণ্ডিতগণ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী দ্রবিড়নাথ ও রাষ্ট্রকূটরাজকে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের কয়েকখানি লিপি হইতে জানা যায় যে, মগধ, কলিঙ্গ, চোল, পল্লব ও গঙ্গ প্রভৃতি রাজ্য মিলিত হইয়া পাণ্ড্যরাজের সহিত যুদ্ধ করে। কুম্বকোন নামক স্থানে পাণ্ড্যরাজ শ্রীমার শ্রীবল্লভ ইহাদের পরাস্ত করেন। শ্রীমার শ্রীবল্লভের রাজ্যকাল ৮৫১ হইতে ৮৬২ অব্দ। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে দেবপাল যে মগধের রাজা ছিলেন সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই; এবং উত্তাল জয় করার পর যে তিনি কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া থাকিবেন ইহাও খুব স্বাভাবিক। সুতরাং অসম্ভব নহে যে উল্লিখিত মিলিত শক্তির সহিত দেবপাল পাণ্ড্যরাজ্যে অবস্থিত। সুতরাং দেবপালের সভাপতি হয়তো এই সমরবিজয় উপলক্ষ করিয়া দেবপালের রাজ্য রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।
দেবপাল অন্তত ৩৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যকাল ৮১০ হইতে ৮৫০ অব্দ অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহার সময়ে পালসাম্রাজ্য গৌরবের চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। তাঁহার রাজত্বকালে বাঙ্গালী সৈন্য ব্রহ্মপুত্র হইতে সিন্ধু নদের তীরে এবং সম্ভবত দক্ষিণ ভারতের প্রায় শেষ প্রান্ত পৰ্য্যন্ত বিজয়াভিযান করিয়াছিল। প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত তাঁহাকে অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিত। ভারতবর্ষের বাহিরেও তাঁহার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল। যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও মলয় উপদ্বীপের অধিপতি শৈলেন্দ্রবংশীয় মহারাজ বালপুত্রদেব তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। শৈলেন্দ্ররাজ প্রসিদ্ধ নালন্দাবিহারে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং ইহার ব্যয় নির্বাহের জন্য পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করেন। তদনুসারে দেবপাল তাঁহাকে পাঁচটি গ্রাম দান করেন। নালন্দা তখন সমগ্র এশিয়ার মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল এবং পালরাজগণও বৌদ্ধধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকরূপে ভারতের বাহিরে সর্বত্র বৌদ্ধগণের নিকট সুপরিচিত ও সম্মানিত ছিলেন। দেবপাল যে নালন্দাবিহারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন অন্য একখানি শিলালিপিতে তাঁহার কিছু আভাস আছে। ইহা হইতে আমরা জানিতে পারি যে নগরহার (বর্ত্তমান জালালাবাদ) নিবাসী ব্রাহ্মণবংশীয় ইন্দ্রগুপ্তের পুত্র বীরদেব “দেবপাল নামক ভুবনাধিপতির নিকট পূজাপ্রাপ্ত” এবং “নালন্দার পরিপালনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।”
৮৫১ অব্দে আরবী ভাষায় লিখিত একখানি গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, তৎকালে ভারতে তিনটি প্রধান রাজ্য ছিল। ইহাদের মধ্যে দুইটি যে রাষ্ট্রকূট ও গুর্জর প্রতীহার তাহা বেশ বুঝা যায়। তৃতীয়টি রুগি অথবা রহ্ম। এই নামের অর্থ বা উৎপত্তি যাহাই হউক ইহা যে পালরাজ্যকে সূচিত করে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। উল্লিখিত গ্রন্থ অনুসারে রক্ষ দেশের রাজা প্রতিবেশী গুর্জর ও রাষ্ট্রকূটরাজার সহিত সৰ্ব্বদাই যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্য শত্রুসৈন্য অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক ছিল। যুদ্ধ যাত্রাকালে ৫০,০০০ রণহস্তী এবং সৈন্যগণের বস্ত্রাদি ধৌত করিবার জন্যই দশ-পনেরো হাজার অনুচর তাঁহার সঙ্গে থাকিত। এই বর্ণনা সম্ভবত দেবপাল সম্বন্ধে প্রযোজ্য।
সোড্ঢল প্রণীত উদয়সুন্দরীকথা নামক কাব্য হইতে জানা যায় যে, অভিনন্দ পালরাজ যুবরাজের সভাপতি ছিলেন। অভিনন্দ প্রণীত রামচরিত কাব্যে যুবরাজের আরও কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ধর্ম্মপালের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং “পালকুলচন্দ্র” এবং “পালকুল প্রদীপ” প্রভৃতি আখ্যায় বিভূষিত হইয়াছেন। তাঁহার উপাধি ছিল হারবর্ষ এবং পিতার নাম বিক্রমশীল। তিনি অনেক রাজ্য জয় করিয়াছিলেন।
যুজরাজ হারবর্ষ যে পালবংশীয় রাজা ছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। বিক্রমশীল ও ধর্ম্মপালেরই নামান্তর তাহাতেও সন্দেহ করিবার বিশেষ কারণ নাই-কারণ তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিহার শ্রীমদ্-বিক্রমশীল-দেব-মহাবিহার নামে অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং যুবরাজ হারবর্ষ ধর্ম্মপালের পুত্র ছিলেন এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু হারবর্ষ যুবরাজ দেবপালেরই নামান্তর অথবা তাঁহার ভ্রাতা এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।
ধর্ম্মপাল ও দেবপালের রাজ্যকালে বাংলার শক্তি ও সমৃদ্ধি কিরূপ বাড়িয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিব্বতদেশীয় গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে ধর্ম্মপাল তিব্বতের রাজা খ্রী স্রং-দে-বৎ সনের (৭৫৫-৭৯৭ অব্দ) বশ্যতা স্বীকার করেন এবং তিব্বতীয় রাজা র-প-চন্ (৮১৭-৮৩৬) গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত জয় করেন। এই প্রকার দাবীর মূলে কত দূর সত্য নিহিত আছে তাহা জানিবার উপায় নাই কারণ ভারতীয় কোনো গ্রন্থ বা লিপিতে উক্ত তিব্বতীয় অভিযানের কোনো উল্লেখ নাই। তবে এরূপ অভিযান অসম্ভব নহে এবং সম্ভবত মাঝে মাঝে ইহার ফলে পালরাজগণ বিপন্ন হইতেন। নাগভট কর্ত্তৃক ধর্ম্মপালের পরাজয় এবং প্রথম ভোজের ৮৩৬ অব্দে কনৌজ অধিকার প্রভৃতি ঘটনার সহিত এরূপ কোনো তিব্বতীয় অভিযানের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সম্বন্ধ থাকা বিচিত্র নহে।
অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল পর্য্যন্ত ধর্ম্মপাল ও দেবপাল আর্য্যাবর্তে বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। অনেকে মনে করেন যে হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্যই আর্য্যাবর্তের শেষ হিন্দু সাম্রাজ্য কিন্তু পালসাম্রাজ্য যে ইহার অপেক্ষা বিস্তৃত ও অধিককাল স্থায়ী হইয়াছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।
প্রাচীন মৌৰ্য্য ও গুপ্তসাম্রাজ্যের সহিত পালসাম্রাজ্যের প্রকৃতিগত প্রভেদ ছিল। মৌর্য ও গুপ্তসাম্রাজ্যের বিস্তৃত ভূভাগ স্বয়ং সম্রাট অথবা তন্নিযুক্ত শাসনকর্ত্তার অধীনে থাকিত। কিন্তু বাংলা ও বিহার ব্যতীত আৰ্য্যাবর্তের অপর কোনো প্রদেশ যে পালরাজগণের বা তাহাদের কর্ম্মচারীর শাসনাধীন ছিল এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। পরাজিত রাজগণ পালরাজগণের অধীনতা ও কোনো কোনো স্থলে করদান করিতে স্বীকার করিলেই সম্ভবত তাঁহারা বিনা বাধায় স্বীয় রাজ্য শাসন করিতে পারিতেন। তাঁহারা পালরাজগণকে উপঢৌকন পাঠাইতেন, মাঝে মাঝে তাঁহাদের সভায় উপস্থিত থাকিতেন এবং সম্ভবত প্রয়োজন হইলে সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতেন। কিন্তু ইহার অতিরিক্ত আর কোনো প্রকার দায়িত্ব সম্ভবত তাঁহাদের ছিল না। এ সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যে প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে তাহা এতই স্বল্প যে নিশ্চিত কোনো প্রকার সিদ্ধান্ত করা কঠিন; তবে হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্য যে এ বিষয়ে পালসাম্রাজ্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ধর্ম্মপাল বা দেবপাল অপেক্ষা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার অধিকতর শক্তি বা ক্ষমতা ছিল এরূপ মনে করিবার কোনোই কারণ নাই।
বাঙ্গালীর বাহুবলে আর্য্যাবর্তে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাই ধৰ্ম্মপাল ও দেবপালের রাজ্যের প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনা। বাঙ্গালীর জাতীয় ইতিহাসে ইহার অনুরূপ শক্তি বা সমৃদ্ধির পরিচয় ইহার পূর্ব্বে বা পরে আর কখনো পাওয়া যায় নাই।
০৭. পালসাম্রাজ্যের পতন
সপ্তম পরিচ্ছেদ –পালসাম্রাজ্যের পতন
দেবপালের মৃত্যুর পর তিনশত বৎসর পর্য্যন্ত পালরাজবংশের ইতিহাস কবি-বর্ণিত “পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায়” অগ্রসর হইয়াছিল। উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে চারিশত বৎসরকাল অতিবাহিত করিয়া অবশেষে এই প্রসিদ্ধ রাজ্য ও রাজবংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ইহাই স্বাভাবিককালের গতি। বরং এত সুদীর্ঘকাল রাজত্বের দৃষ্টান্ত আৰ্য্যাবর্তের ইতিহাসে অতি বিরল, নাই বলিলেও চলে।
দেবপালের মৃত্যুর পর বিগ্রহপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন। দেবপাল ও বিগ্রহপালের সম্বন্ধ লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কাহারও মতে বিগ্রহপাল দেবপালের পুত্র। কিন্তু অধিকাংশ পণ্ডিতগণই মনে করেন যে বিগ্রহপাল ধৰ্ম্মপালের ভ্রাতা বাপালের পৌত্র ও জয়পালের পুত্র। এই মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হয় এবং বিগ্রহপালের পুত্র নারায়ণপালের তাম্রশাসনে পালরাজগণের যে বংশাবলী বিবৃত হইয়াছে তাহাও এই মতের সমর্থন করে। ইহাতে তৃতীয় শ্লোকে ধর্ম্মপালের বর্ণনার পরে চতুর্থ শ্লোকে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাপালের ও পঞ্চম শ্লোকে তাঁহার পুত্র জয়পালের উল্লেখ আছে। এই শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে জয়পাল ধর্ম্মদ্বেষিগণকে যুদ্ধে বশীভূত করিয়া পূৰ্ব্বজ দেবপালকে ভুবনরাজ্যসুখের অধিকারী করিয়া দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী ষষ্ঠ শ্লোকে জয়পাল কর্ত্তৃক উকল ও কামরূপ জয় বর্ণিত হইয়াছে। সপ্তম শ্লোকে বলা হইয়াছে তাঁহার অজাতশত্রুর ন্যায় বিগ্রহপাল নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সংস্কৃতি রচনানীতি অনুসারে তাঁহার এই সর্বনাম শব্দ নিকটবর্ত্তী বিশেষ্য পদকেই সূচিত করে। সুতরাং পঞ্চম ও সপ্তম শ্লোকের ‘তাঁহার’ এই সর্বনাম শব্দ যথাক্রমে বাপাল ও জয়পাল সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে ইহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। অতএব বাপালের পুত্রই যে জয়পাল, এবং জয়পালের পুত্র বিগ্রহপাল, উক্ত দুই শ্লোক হইতে এইরূপ সিদ্ধান্ত হয়। অপর পক্ষ বলেন যে, দেবপাল জয়পালের পূৰ্ব্বজ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, সুতরাং জয়পাল দেবপালের কনিষ্ঠ সহোদর অর্থাৎ ধর্ম্মপালের পুত্র। অতএব পঞ্চম ও সপ্তম শ্লোকের ‘তাঁহার’ এই সৰ্ব্বনাম শব্দ যথাক্রমে ধর্ম্মপাল ও দেবপালের সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। এই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না, কারণ পূৰ্ব্বজ শব্দে কেবল জ্যেষ্ঠ বুঝায়, জ্যেষ্ঠ সহোদর অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। অপর পক্ষে ইহাও বিবেচ্য যে ধর্ম্মপাল বা দেবপালের তাম্রশাসনে বাপালের বা জয়পালের কোনো উল্লেখ নাই, সহসা নারায়ণপালের তাম্রশাসনে তাঁহাদের এই গুণ-ব্যাখ্যানের হেতু কী? ইহার একমাত্র সঙ্গত কারণ এই মনে হয় যে বিগ্রহপাল ও তাঁহার বংশধরগণ দেবপালের ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী ছিলেন না, সুতরাং তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কৃতিত্ব দ্বারাই তাঁহাদের সিংহাসন অধিকারের সমর্থন করার প্রয়োজন ছিল। অন্যথা তিন পুরুষ পরে এই প্রাচীন কীর্তিগাথা উদ্ধারের আর কোনো যুক্তি পাওয়া যায় না।
দেবপালের কোনো পুত্র না থাকায় বিগ্রহপাল পিতৃব্যের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন ইহা খুব সম্ভব বলিয়া মনে হয় না, কারণ দেবপালের রাজ্যের ৩৩ বর্ষে অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর অনধিকাল পূর্ব্বের উৎকীর্ণ একখানি তাম্রশাসনে তাঁহার পুত্র রাজ্যপালের যৌবরাজ্যে অভিষেকের উল্লেখ আছে। অবশ্য পিতার জীবিতকালেই রাজ্যপালের মৃত্যু হইয়া থাকিতে পারে। কিন্তু ইহাও অসম্ভব নহে যে সেনাপতি জয়পাল বৃদ্ধ রাজা দেবপালের মৃত্যুর পর অনুগত সৈন্যবলের সাহায্যে নিজের পুত্রকেই সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। দেবপালের মৃত্যুর পরই যে পালরাজ্য ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছিল হয়তো এই গৃহবিবাদই তাঁহার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে উপযুক্ত প্রমাণ না থাকায় নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।
বিগ্রহপাল শূরপাল নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি শান্তিপ্রিয় ও সংসারবিরাগী ছিলেন। অল্পকাল (আ ৮৫০-৮৫৪) রাজ্য করিয়াই তিনি পুত্র নারায়ণপালের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন। নারায়ণপাল সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করেন (আ ৮৫৪-৯০৮)। তাঁহার ৫৪ রাজ্যসংবৎসরের একখানি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তিনিও পিতার ন্যায় উদ্যমহীন শান্তিপ্রিয় ছিলেন। কেদারমিশ্রের পুত্র গুরবমিশ্র তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। এই গুরবমিশ্রের লিপিতে ধর্ম্মপাল ও দেবপালের অনেক রাজ্যজয়ের উল্লেখ আছে। কিন্তু বিগ্রহপাল ও নারায়ণপাল সম্বন্ধে সেরূপ কোনো উক্তি নাই। রাজা শূরপাল সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে তিনি কেদারমিশ্রের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া অনেকবার শ্রদ্ধাবনতশিরে পবিত্র শান্তিবারি গ্রহণ করিয়াছিলেন।
ধর্ম্মপাল ও দেবপাল বাহুবলে যে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন যজ্ঞের শান্তিবারি বা তপস্যা দ্বারা তাহা রক্ষা করা সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং বিগ্রহপাল ও নারায়ণপালের অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককালব্যাপী রাজ্যকালে বিশাল পালসাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গেল, এমনকি বিহার ও বাংলা দেশের কোনো কোনো অংশও বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল।
রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষের লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধের অধিপতি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। আ ৮৬০ অব্দে অমোঘবর্ষ কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্ত্তী বেঙ্গি দেশ জয় করেন। সম্ভবত ইহার অনতিকাল পরেই তিনি পালরাজ্য আক্রমণ করেন। অঙ্গ বঙ্গ ও মগধের পৃথক উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে এগুলি তখন পৃথক স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল-কিন্তু এ অনুমান সত্য না-ও হইতে পারে। সম্ভবত পালরাজ পরাজিত হইয়াছিলেন-কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ যে স্থায়ীভাবে এ দেশের কোনো অংশ অধিকার করিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। তবে এই পরাজয়ে পালরাজগণের খ্যাতি ও প্রতিপত্তির অনেক লাঘব হইয়াছিল এবং সম্ভবত এই সুযোগে উড়িষ্যার শুক্তিবংশীয় মহারাজাধিরাজ রণস্তম্ভ রাঢ়ের কিয়দংশ অধিকার করেন।
পালরাজ যখন এইরূপে দক্ষিণ দিক হইতে আগত শত্রুর আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত তখন প্রতীহাররাজ ভোজ পুনরায় আৰ্য্যাবর্তে স্বীয় প্রাধান্য স্থাপনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। যত দিন দেবপাল জীবিত ছিলেন তত দিন তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। কিন্তু নারায়ণপালের ন্যায় দুৰ্বল রাজার পক্ষে ভোজের গতিরোধ করা সম্ভবপর হইল না। ভোজ কলচুরি ও গুহিলোট রাজগণের সহায়তায় নারায়ণপালকে গুরুতররূপে পরাজিত করিলেন। পালসাম্রাজ্যের ধ্বংসের উপর প্রতীহার রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইল। ভোজের পুত্র মহেন্দ্রপাল পুনরায় পালরাজ্য আক্রমণ করিয়া বিহার প্রদেশ অধিকার করেন। তারপর অগ্রসর হইয়া ক্রমে তিনি উত্তর বাংলায় স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিলেন। বাংলা ও বিহারে মহেন্দ্রপালের যে সমুদয় লিপি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের তারিখ ৮৮৭ হইতে ৯০৪ অব্দের মধ্যে। কলচুরিরাজ কোক্কলুও সম্ভবত এই সময়ে বঙ্গ আক্রমণ করিয়া ইহার ধনরত্ন লুণ্ঠন করেন।
এইরূপে নবম শতাব্দের শেষভাবে কেবলমাত্র আর্য্যাবর্তের বিস্তৃত সাম্রাজ্য নহে, পালরাজগণের নিজ রাজ্যও শত্রুর করতলগত হইল। নারায়ণপালের অক্ষমতা ব্যতীত হয়তো এইরূপ শোচনীয় পরিণামের অন্য কারণও বিদ্যমান ছিল। দেবপালের মৃত্যুর পর পালরাজবংশের গৃহবিবাদের কথা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণ (আ ৮৮০-৯১৪) পালরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। বিজিত কামরূপ ও উৎকলের রাজগণ এই সময়ে প্রবল হইয়া ওঠেন এবং সম্ভবত তাঁহাদের সহিতও নারায়ণপালের সংগ্রাম হইয়াছিল। এইরূপে আভ্যন্তরিক কলহ ও চতুর্দিকে বহিঃশত্রুর আক্রমণে পালরাজ্যের দুর্দশা চরমে পৌঁছিয়াছিল।
পালরাজগণ আৰ্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্যের দুইটি প্রবল রাজবংশের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিগ্রহপাল কলচুর অথবা হৈহয় রাজবংশের কন্যা লজ্জাদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কলচুরিগণ নারায়ণপালের শত্রুপক্ষে যোগদান করিয়াছিল।
নারায়ণপালের পুত্র রাজ্যপাল রাষ্ট্রকৃটরাজ তুঙ্গের কন্যা ভাগ্যদেবীকে বিবাহ করেন। এই তুঙ্গ সম্ভবত দ্বিতীয় কৃষ্ণের পুত্র জগঙ্গ। এই বিবাহের ফলে পালরাজগণের কিছু সুবিধা হইয়াছিল কি না জানা যায় না। কিন্তু নারায়ণপালের সুদীর্ঘ রাজ্যের শেষে তিনি প্রতীহারগণকে দূর করিয়া পুনরায় বিহার ও বাংলায় স্বীয় প্রাধান্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।
নারায়ণপালের মৃত্যুর পর যথাক্রমে তাঁহার পুত্র রাজ্যপাল (আ ৯০৮ ৯৪০) ও তৎপুত্র দ্বিতীয় গোপাল (আ ৯৪০-৯৬০) রাজত্ব করেন। পালরাজগণের সভাকবি লিখিয়াছেন যে রাজ্যপাল সমুদ্রের ন্যায় গভীর জলাশয় খনন ও পৰ্ব্বতের তুল্য উচ্চ মন্দির নির্মাণ করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি রাজ্যপাল ও গোপালের কোনোরূপ বিজয়কাহিনীর উল্লেখ করেন নাই। রাজ্যপাল সম্ভবত নিরুদ্বেগে রাজত্ব করিতে পারিয়াছিলেন। কারণ তাঁহার রাজ্যের প্রারম্ভেই চিরশত্রু প্রতীহাররাজ রাষ্ট্রকূটরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল। ইন্দ্র প্রতীহার রাজধানী কান্যকুব্জ অধিকার করিয়া লুণ্ঠন করিয়াছিল এবং প্রতীহাররাজ মহীপাল পলাইয়া কোনোমতে প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। এই নিদারুণ বিপর্যয়ের ফলে প্রতীহার রাজ্য ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইল এবং পালরাজগণও অনেকটা নিরাপদ হইলেন।
কিন্তু শীঘ্রই অন্য শত্রুর আবির্ভাব হইল। পাল ও প্রতীহার সাম্রাজ্যের পতনের পরে আর্য্যাবর্তে নূতন নূতন রাজশক্তির উদয় হইল এবং ইহারা অনেকেই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় পাল, প্রতীহার ও অন্যান্য রাজ্যের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইল। এইরূপে সর্বপ্রথমে মধ্যভারতের বুন্দেলখণ্ড অঞ্চলে চন্দ্রাত্রেয় বা চল্লে রাজ্য প্রবল হইয়া ওঠে। চন্দেল্লরাজ যশোবৰ্মণ প্রসিদ্ধ কালঞ্জয় গিরিদুর্গ অধিকার করিয়া আৰ্য্যাবর্তে প্রাধান্য লাভ করেন এবং তাঁহার বিজয়বাহিনী কাশ্মীর হইতে বাংলা দেশ পর্য্যন্ত যুদ্ধাভিযান করে। চন্দেল্লরাজের সভাকবি লিখিয়াছেন যে যশোবর্ম্মণ গৌড়দিগকে উদ্যানলতার ন্যায় অবলীলাক্রমে অসি দ্বারা ছেদন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র ধঙ্গ (আ ৯৫৪-১০০০) রাঢ়া ও অঙ্গদেশের রাণীকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সমুদয় শ্লেষোক্তি নিছক সত্য না হইলেও পালরাজগণ চন্দেল্লরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন ইহাই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। চন্দেল্লগণের ন্যায় কলচুরি রাজগণও দশ শতাব্দের মধ্যভাগে আর্য্যাবর্তে নানা দেশ আক্রমণ করেন। কলচুরিরাজ প্রথম যুবরাজ ও তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণরাজ যথাক্রমে গৌড় ও বঙ্গাল দেশ জয় করেন বলিয়া তাহাদের সভাকবি বর্ণনা করিয়াছেন।
এই সমুদয় আক্রমণের ফলে পালরাজগণ ক্রমেই শক্তিহীন হইয়া পড়িলেন এবং বাংলা দেশের বিভিন্ন অংশে স্বাধীন খণ্ডরাজ্যের উদ্ভব হইল। চন্দেল্ল ও কলচুরি রাজবংশের সভাকবিরা যে অঙ্গ, রাঢ়া, গৌড় ও বঙ্গাল প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সম্ভবত এইরূপ পৃথক পৃথক স্বাধীন রাজ্যের সূচনা করে। কিন্তু ইহার অন্যবিধ প্রমাণও আছে।
দ্বিতীয় গোপালের পুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল আ ৯৬০ হইতে ৯৮৮ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র মহীপালের তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে তিনি (মহীপাল) অনধিকারী কর্ত্তৃক বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করেন। সুতরাং দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালেই পালগণের পৈত্রিক রাজ্যের বিলোপ হইয়াছিল। উত্তরবঙ্গের একখানি শিলালিপি ও পশ্চিমবঙ্গের একখানি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, এই সময়ে এই দুই প্রদেশে কাম্বোজবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। সুতরাং এই কাম্বোজ রাজগণই যে মহীপালের তাম্ৰশাসনোক্ত ‘অনধিকারী’ তাহা নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায়।
বাংলার এই কাম্বোজ রাজবংশের উৎপত্তি গভীর রহস্যে আবৃত। ইহার প্রতিষ্ঠাতা মহারাজাধিরাজ রাজ্যপাল কামোজ-বংশ-তিলক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার রাণীর নাম ভাগ্যদেবী। তাঁহার পর তাঁহার দুই পুত্র নারায়ণপাল ও নয়পাল যথাক্রমে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রিয় নামক নগরে নয়পালের রাজধানী ছিল।
বাংলার পালসম্রাট নারায়ণপালের পুত্র রাজ্যপালের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার রাণীর নামও ভাগ্যদেবী। এইরূপ নামসাদৃশ্য হইতে এই দুই রাজ্যপালকে অভিন্ন মনে করা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা হইলে ‘কাম্বোজবংশ তিলক’ এই উপাধির সার্থকতা কী? কেহ কেহ অনুমান করেন যে পালসম্রাট রাজ্যপালের মাতা সম্ভবত কাম্বোজবংশীয়া রাজকন্যা ছিলেন এবং সেই জন্যই রাজ্যপাল কাম্বোজবংশ-তিলক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এরূপ মাতৃবংশ দ্বারা পরিচয়ের দৃষ্টান্ত অন্যান্য রাজবংশের ইতিহাসেও পাওয়া যায়। এই দুই রাজ্যপালের অভিন্নতা মানিয়া লইলে এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে তাঁহার মৃত্যুর পর রাজ্যের এক অংশে (অঙ্গ ও মগধে) তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় গোপাল ও তৎপুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল ও অন্য অংশে (উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে) তাঁহার দুই পুত্র নারায়ণপাল ও নয়পাল যথাক্রমে রাজত্ব করেন। অন্যথা স্বীকার করিতে হয় যে রাজ্যপাল নামক কাম্বোজবংশীয় এক ব্যক্তি কোনো উপায়ে পালরাজগণের হস্ত হইতে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ অধিকার করিয়া একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন।
ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে কামোজ জাতির আদি বাসস্থল। এই সুদূর দেশ হইতে আসিয়া কামোজ জাতি বাংলা দেশ জয় করিয়াছিল ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। তিব্বতীয়েরা কোনো কোনো গ্রন্থে কাম্বোজ নামে অভিহিত হইয়াছে এবং কোনো কোনো তিব্বতীয় গ্রন্থে লুসাই পৰ্ব্বতের নিকটবর্ত্তী বঙ্গ ও ব্রহ্মদেশের সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত কাম্বোজ জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, যে কামোজ জাতি বাংলা দেশ জয় করিয়াছিল তাহা এ দুয়ের অন্যতম। কিন্তু কাম্বোজ জাতি যে বাংলা দেশ আক্রমণ করিয়া জয় করিয়াছিল এরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিবার কোনো কারণ নাই। পালরাজগণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতেন। দেবপালের লিপি হইতে জানা যায় যে, কাম্বোজ দেশ হইতে পালরাজগণের যুদ্ধ-অশ্ব সংগৃহীত হইত। সুতরাং অসম্ভব নহে যে কামোজদেশীয় রাজ্যপাল পালরাজাগণের অধীনে সৈন্য অথবা অন্য কোনো বিভাগে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং পালরাজগণের দুর্বলতার সুযোগে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। যে উপায়েই কাম্বোজ রাজবংশ প্রতিষ্ঠা হউক, দশম শতাব্দের মধ্যভাগে যে তাঁহাদের অধীনে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।
বাংলার অন্যান্য অঞ্চলেও কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। মহারাজাধিরাজ কান্তিদেব হরিকেলে রাজত্ব করিতেন এবং তাঁহার রাজধানীর অথবা এক প্রধান নগরীর নাম ছিল বর্দ্ধমানপুর। হরিকেল বলিতে সাধারণত পূৰ্ব্ববঙ্গ বুঝায় কিন্তু ইহা বঙ্গের নামান্তররূপেও ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং কান্তি দেবের রাজ্য কোথায় এবং কত দূর বিস্তৃত ছিল বলা যায় না। যদি বর্দ্ধমানপুর সুপরিচিত বর্দ্ধমান নগরী হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে যে কান্তিদেবের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গেও বিস্তৃত ছিল। কান্তিদেব বিন্দুরতি নাম্নী এক শক্তিশালী রাজার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন এবং সম্ভবত ইহাই তাঁহার সৌভাগ্যের মূল। কারণ তাঁহার পিতা বা পিতামহ রাজা ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কান্তিদেব কোন সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা সঠিক নির্ণয় করা যায় না। খুব সম্ভবত দেবপালের পরবর্ত্তী দুৰ্বল পালরাজগণের সময়েই তিনি পূর্ব্ববঙ্গে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। পরে দক্ষিণ বাংলা ও সম্ভবত পশ্চিম বাংলার কিয়দংশও অধিকার করেন। দশম শতাব্দী হইতে যে বঙ্গাল রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় সম্ভবত কান্তিদেবই তাঁহার পত্তন করেন। কান্তিদেব বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণের সম্বন্ধে এ পৰ্য্যন্ত কিছুই জানা যায় নাই।
কান্তিদেবের অনতিকাল পরেই লয়হচন্দ্রদেব কুমিল্লা অঞ্চলে রাজত্ব করেন। তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। কিন্তু চন্দ্ৰ উপাধিধারী এক বৌদ্ধ রাজবংশ দশম শতাব্দের শেষভাগে হরিকেলে রাজত্ব করিতেন। চন্দ্রদ্বীপ তাঁহাদের রাজ্যভুক্ত ছিল এবং সম্ভবত রাজবংশের উপাধি হইতেই এই নামকরণ হইয়াছিল। লামা তারনাথ চন্দ্রবংশীয় রাজাদের বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন কিন্তু তাঁহার মতে এই সকল রাজাই পালরাজগণের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন। দশম শতাব্দীতে বাংলায় যে চন্দ্রবংশ রাজত্ব করিতেন তাঁহাদের সহিত তারনাথ বর্ণিত চন্দ্রবংশের অথবা আরাকানে চন্দ্ৰ উপাধিধারী যে সমুদয় রাজগণ রাজত্ব করিয়াছেন তাহাদের কোনো সম্বন্ধ ছিল কি না তাহা অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। আলোচ্য চন্দ্রবংশের মাত্র দুইজন রাজার নাম এ পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে–মহারাজাধিরাজ ত্রৈলোক্যচন্দ্র ও তাঁহার পুত্র মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্র। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পিতা সুবর্ণচন্দ্র ও পিতামহ পূর্ণচন্দ্রের সম্বন্ধে আমরা কেবলমাত্র এইটুকু জানি যে তাঁহারা অথবা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ রোহিতাগিরিতে রাজত্ব করিতেন। ত্রৈলোক্যচন্দ্ৰই প্রথমে হরিকেলে ও চন্দ্রদ্বীপে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। রোহিতাগিরি কোথায় ছিল ঠিক বলা যায় না। কেহ কেহ মনে করেন যে ইহাই বর্ত্তমানে রোটা গড় নামে পরিচিত। আবার কাহারও মতে কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী লালমাই অথবা লালমাটি সংস্কৃত রোহিতাগিরিতে পরিণত হইয়াছে। চন্দ্রবংশের আদিম নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে ছিল ইহাই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। এই পর্য্যন্ত এ বংশের যে পাঁচখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহা বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত। সুতরাং বিক্রমপুর তাঁহাদের রাজধানী ছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। বাংলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজধানী বিক্রমপুর সম্ভবত চন্দ্রবংশীয় রাজারাই প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীনকালে বঙ্গ ও বঙ্গাল বলিলে যে দেশ বুঝাইত ত্রৈলোক্যচন্দ্র ও শ্রীচন্দ্র তাঁহার রাজা ছিলেন। শ্রীচন্দ্র অন্তত ৪৪ বৎসর রাজত্ব করেন। সম্ভবত তাঁহার রাজ্যকালেই কলচুরিরাজ লক্ষ্মণরাজ বঙ্গাল দেশ আক্রমণ করেন।
একাদশ শতাব্দের প্রারম্ভে গোবিন্দচন্দ্র দক্ষিণ ও পূৰ্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেন। চোলরাজ রাজেন্দ্ৰচোলের লিপিতে তিনি বঙ্গাল দেশের রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, কিন্তু বিক্রমপুরেও তাঁহার দ্বাদশ ও এয়োবিংশ রাজ্যাব্দের দুইখানি লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গোবিন্দচন্দ্র সম্ভবত চন্দ্রবংশীয় রাজা, কিন্তু শ্রীচন্দ্রের সহিত তাঁহার কী সম্বন্ধ ছিল তাহা জানা যায় নাই।
উল্লিখিত আলোচনা হইতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে দ্বিতীয় গোপাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালে পালরাজ্য তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। পূৰ্ব্ব ও দক্ষিণবঙ্গ অর্থাৎ বঙ্গ ও বঙ্গাল দেশে চন্দ্রবংশীয় রাজ্য, পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ অর্থাৎ রাঢ়া ও বরেন্দ্রে অথবা গৌড়ে কাম্বোজবংশীয় রাজ্য, এবং বিহার অর্থাৎ অঙ্গ ও মগধে পালবংশীয় রাজ্য। এতদ্ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গে আরও দু-একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল, তাহা পরে আলোচিত হইবে। এই সময় পালরাজগণের পিতৃভূমি বিশাল বাংলা দেশে তাঁহাদের কোনো প্রকার অধিকার ছিল বলিয়া মনে হয় না।
চন্দ্রেল্ল ও কলচুরি রাজগণের প্রশস্তিতে যে বঙ্গ, বঙ্গাল, গৌড়, রাঢ়া, অঙ্গ প্রভৃতি রাজ্য জয়ের উল্লেখ আছে তাহা খুব সম্ভবত এই সমুদয় স্বাধীন খণ্ডরাজ্যের প্রতি প্রযোজ্য।
০৮. দ্বিতীয় পালসাম্রাজ্য
অষ্টম পরিচ্ছেদ –দ্বিতীয় পালসাম্রাজ্য
১. মহীপাল
দশম শতাব্দের শেষভাগে যখন পালরাজবংশ দুর্দশা ও অবনতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল তখন দ্বিতীয় বিগ্রহপালের পুত্র মহীপাল পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন (আ ৯৮৮)। তাঁহার অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী রাজ্যকালে পালরাজবংশের সৌভাগ্যরবি আবার উদিত হইয়াছিল। তিনি বাংলায় বিলুপ্ত পিতৃরাজ্য উদ্ধার ও পুনরায় পালসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া যে অতুল কীৰ্ত্তি অর্জন করিয়াছেন তাহা ইতিহাসে তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। বাংলা দেশ ধর্ম্মপাল ও দেবপালের নাম ভুলিয়া গিয়াছে কিন্তু ‘ধান ভানতে মহীপালের গীত’ প্রভৃতি লৌকিক প্রবাদ, দিনাজপুরের মহীপালদীঘি এবং মহীপাল, মহীপুর, মহীসন্তোষ প্রভৃতি স্থান আজিও মহীপালের স্মৃতি রক্ষা করিয়া আসিতেছে।
কুমিল্লা নিকটবর্ত্তী বাঘাউড়া ও নারায়ণপুর গ্রামে একটি বিষ্ণু ও একটি গণেশ মূর্ত্তির পাদপীঠে যথাক্রমে তৃতীয় ও চতুর্থ সংবৎসরে উত্তীর্ণ মহীপালের দুইখানি লিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে সিংহাসনে আরোহণের ২-৩ বৎসরের মধ্যেই তিনি পূর্ব্ববঙ্গ পুনরাধিকার করিয়াছিলেন। উত্তর অথবা পশ্চিমবঙ্গ জয় না করিয়া তিনি পূৰ্ব্ববঙ্গে যাইতে পারেন নাই। তাঁহার রাজত্বের নবম বৎসরে উত্তীর্ণ বাণগড় লিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে উত্তরবঙ্গ তাঁহার অধীন ছিল। সুতরাং রাজ্যারম্ভেই তিনি উত্তর ও পূৰ্ব্ববঙ্গ জয় করেন এই সিদ্ধান্ত অনায়াসে করা যাইতে পারে। বাণগড় লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে মহীপাল ‘রণক্ষেত্রে বাহুদর্পপ্রকাশে সকল বিপক্ষ পক্ষ নিহত করিয়া অনধিকারী কর্ত্তৃক বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়া, রাজগণের মস্তকে চরণপদ্ম সংস্থাপিত করিয়া, অবনিপাল হইয়াছিলেন।’ সভাকবির এই উক্তি যে ঐতিহাসিক সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।
কিন্তু সমগ্র বাংলা দেশ জয় করিবার পূর্ব্বেই দক্ষিণ ভারতের পরাক্রান্ত চোলরাজ রাজেন্দ্র মহীপালের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। চোলরাজগণের ন্যায় শক্তিশালী রাজবংশ তখন ভারতবর্ষে আর ছিল না। উড়িষ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া রামেশ্বর সেতুবন্ধ পৰ্য্যন্ত ভারতের পূর্ব্ব উপকূল সমস্তই তাঁহাদের অধীন ছিল, এবং তাঁহাদের প্রচণ্ড ও প্রকাণ্ড নৌবাহিনী বঙ্গোপসাগরের পরপারে সুমাত্রা ও মলয় উপদ্বীপের বহু রাজ্য জয় করিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বিপুল বাণিজ্যভাণ্ডারের স্বর্ণদ্বার তাঁহাদের সম্মুখে উক্ত করিয়া দিয়াছিল। এই বিশাল সাম্রাজ্য ও অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী রাজা রাজেন্দ্রচোল শিবের উপাসক ছিলেন। সুতরাং তাঁহার রাজ্য পবিত্র করিবার উদ্দেশে গঙ্গাজল আনয়ন করিবার জন্য তিনি এক বিরাট সৈন্যদল প্রেরণ করেন। তাঁহার সেনাপতি বঙ্গের সীমান্তে উপস্থিত হইয়া প্রথমে দণ্ডভুক্তিরাজ ধর্ম্মপাল ও পরে লোকপ্রসিদ্ধ দক্ষিণ রাঢ়ের অধিপতি রণশূরকে পরাজিত করিয়া এই দুই রাজ্য অধিকার করেন। তারপর তিনি ‘অবিরাম-বর্ষা বারি-সিক্ত’ বঙ্গাল দেশ আক্রমণ করিলে রাজা গোবিন্দচন্দ্র হস্তীপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। তারপর শক্তিশালী মহীপালের সহিত যুদ্ধ হইল। মহীপাল ভীত হইয়া রণস্থল ত্যাগ করিলেন এবং তাঁহার দুর্মদ রণহস্তী, নারীগণ ও ধনরত্ন লুণ্ঠণপূৰ্ব্বক চোলসেনাপতি উত্তর রাঢ় অধিকার করিয়া গঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন।
চোলারাজের সভাকবি এই অভিযানের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে অনুমিত হয় যে গঙ্গাজল সংগ্রহ করা ছাড়া ইহার আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। তামিল ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করেন যে এই অভিযানে আর কোনো স্থায়ী ফল লাভ হয় নাই। চোল প্রশস্তিতে বাংলায় চোলরাজ্যের প্রভুত্ব বা প্রতিষ্ঠার কোনো উল্লেখ নাই, কেবল বলা হইয়াছে যে চোলসেনাপতি বাংলার পরাজিত রাজন্যবর্গকে মস্তকে গঙ্গাজল বহন করিয়া আনিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ইহা সত্য হইলে বলিতে হইবে যে পৃথিবীতে অন্ধ ধৰ্ম্মবিশ্বাসের জন্য যত উৎপীড়ন ও অত্যাচার হইয়াছে চোলরাজ্যের বঙ্গদেশ আক্রমণ তাঁহার এক চরম দৃষ্টান্ত। বিনা যুদ্ধে বাংলার রাজগণ যে চোলরাজাকে গঙ্গাজল দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন ইহা চোল প্রশস্তি কার বলেন নাই এবং ইহা স্বভাবতই বিশ্বাস করা কঠিন। সুতরাং ইহার জন্য অনর্থক সহস্র সহস্র লোক হত্যা করা ধর্ম্মের নামে গুরুতর অধৰ্ম্ম বলিয়াই মনে হয়। অপর পক্ষে দিগ্বিজয়ী রাজেন্দ্রচোল যে কেবল গঙ্গাজলের জন্যই সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, বঙ্গদেশ জয় করা তাঁহার মোটেই উদ্দেশ্য ছিল না, ইহাও বিশ্বাস করা কঠিন। হয়তো এই চেষ্টা সফল হয় নাই বলিয়াই চোলরাজের সভাকবি পরাজয় ও ব্যর্থতার কলঙ্ক গঙ্গাজল দিয়া ধুইয়া ফেলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আৰ্য্য ক্ষেমীশ্বর প্রণীত চণ্ডকৌশিক নাটকে মহীপাল কর্ত্তৃক কর্ণাটগণের পরাভবের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পালরাজ মহীপাল চোলসৈন্যকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মত গ্রহণ করা কঠিন। কারণ চোল ও কর্ণাট দুই ভিন্ন দেশ। সম্ভবত প্রতীহাররাজ মহীপাল কর্ত্তৃক রাষ্ট্রকূট সৈন্যের পরাভবের কথাই চণ্ডকৌশিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে, কারণ রাষ্ট্রকূটগণ কর্ণাট দেশে রাজত্ব করিতেন।
রাজেন্দ্ৰচোলের অভিযানের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও ফলাফল যাহাই হউক মোটের উপর একথা সকলেই স্বীকার করেন যে ভাগীরথীর পবিত্র বারি সগ্রহ করিয়া চোলসৈন্যের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের পর বাংলা দেশে তাঁহাদের বিজয় অভিযানের আর কোনো চিহ্ন রহিল না। তামিল প্রশস্তিকারের উল্লিখিত বর্ণনা হইতে মনে হয় যে দণ্ডভুক্তি, দক্ষিণ রাঢ় ও বঙ্গালদেশে তখন ধৰ্ম্মপাল, রণশূর ও গোবিন্দচন্দ্র স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন-কিন্তু উত্তর রাঢ় মহীপালের অধীন ছিল। চোল আক্রমণের ফলে এই রাজনৈতিক অবস্থার কোনো পরিবর্ত্তন হইয়াছিল কি না এবং মহীপাল দক্ষিণ রাঢ় ও দক্ষিণবঙ্গ জয় করিয়া সমগ্র বঙ্গে তাঁহার অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন কি না তাহা ঠিক জানা যায় না।
মহীপালের পিতা ও পিতামহ মগধে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু মিথিলাও (উত্তর বিহার) মহীপালের রাজ্যভুক্ত ছিল। সম্ভবত মহীপাল নিজেই মিথিলা জয় করিয়াছিলেন।
বারাণসীর নিকটবর্ত্তী প্রাচীন বৌদ্ধতীর্থ সারনাথে ১০৮৩ সংবতে (১০২৬) উৎকর্ণ একখানি লিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে গৌড়াধিপ মহীপালের আদেশে তাঁহার অনুজ শ্ৰীমান স্থিরপাল ও শ্রীমান বসন্তপাল কর্ত্তৃক নূতন নূতন মন্দির নিৰ্ম্মাণ ও পুরাতন মন্দিরাদির জীর্ণসংস্কারের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে ১০২৬ অব্দে মহীপালের অধিকার বারাণসী পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।
কিন্তু ইহার অল্পকাল পরেই কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেব মহীপালকে পরাজিত করিয়া বারাণসী অধিকার করেন। কারণ ১০৩৪ খৃষ্টাব্দে যখন আহম্মদ নিয়ালতিগীন বারাণসী আক্রমণ করেন তখন ইহা কলচুরিরাজের অধীন ছিল।
মহীপালের রাজ্যকালে আর্য্যাবর্তের পশ্চিমভাগে বড়ই দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছিল। গজনীর সুলতানগণের পুনঃপুন ভারত আক্রমণের ফলে পরাক্রান্ত সাহি ও প্রতীহারবংশের ধ্বংস হয়, অন্যান্য রাজবংশ বিপর্যস্ত ও হতবল হইয়া পড়েন এবং ভারতের প্রসিদ্ধ মন্দির ও নগরগুলি ধ্বংস ও তাহাদের অগণিত ধনরত্ন লুণ্ঠিত হয়। আর্য্যাবর্তের রাজন্যবর্গ একযোগে তাহাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াও কোনো ফল লাভ করিতে পারেন নাই। এই বিধর্মী বিদেশী শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য মহীপাল কোনো সাহায্য প্রেরণ করেন নাই, এজন্য কোনো এক ঐতিহাসিক তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন। কিন্তু মহীপালের ইতিহাস সম্যক্ আলোচনা করিলে এই প্রকার নিন্দা বা অভিযোগের সমর্থন করা যায় না। পিতৃরাজ্যচ্যুত মহীপালকে নিজের বাহুবলে বাংলায় পুনরাধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। এই কাৰ্য্য সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই রাজেন্দ্রচোল তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। কলচুরিরাজও তাঁহার আর এক শত্রু ছিলেন। তৎকালে রাজেন্দ্রচোল ও গাঙ্গেয়দেবের ন্যায় দিগ্বিজয়ী বীর ভারতবর্ষে আর কেহ ছিল না। ইহাদের ন্যায় শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতেই তাহাকে সর্বদা বিব্রত থাকিতে হইত। এমতাবস্থায় সুদূর পঞ্চনদে সৈন্য প্রেরণ করা তাঁহার পক্ষে হয়ত সম্ভব ছিল না। সুতরাং তৎকালীন বাংলার অভ্যন্তরীণ অবস্থা সবিশেষ না জানিয়া মহীপালকে ভীরু, কাপুরুষ অথবা দেশের প্রতি কর্তব্যপালনে উদাসীন ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।
মহীপাল যাহা করিয়াছিলেন তাহাই তাঁহার শৌর্যবীর্যের যথেষ্ট পরিচয় দিতেছে। পালরাজ্যকে আসন্ন ধ্বংসের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া তিনি বঙ্গদেশের পূৰ্ব্ব সীমান্ত হইতে রাবাণসী পৰ্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ ও মিথিলায় পালরাজ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তারপর ভারতের দুই প্রবল রাজশক্তির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া তিনি এই রাজ্যের অধিকাংশ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহাই মহীপালের কৃতিত্বের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।
পালরাজশক্তির পুনরাভ্যুদয়ের চিহ্নস্বরূপ মহীপাল প্রাচীন কীর্তির রক্ষণে যত্নশীল ছিলেন। সারনাথ লিপিতে শত শত কীর্তিরত্ন নির্মাণ এবং অশোকস্তূপ, সাঙ্গধর্ম্মচক্র ও “অষ্টমহাস্থান” শৈলবিনির্ম্মিত গন্ধকুটি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রাচীন বৌদ্ধকীৰ্ত্তির সংস্কার সাধনের উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত মহীপাল অগ্নিদাহে বিনষ্ট নালন্দা মহাবিহারের জীর্ণোদ্ধার এবং বৌদ্ধগয়ায় দুইটি মন্দির নির্মাণ করেন। কাশীধামে নবদুর্গার প্রাচীন মন্দির ও অন্যান্য হিন্দু দেব-দেবীর মন্দিরও সম্ভবত তিনি নির্মাণ করেন। অনেক দীর্ঘিকা ও নগরী এখনো তাঁহার নামের সহিত বিজড়িত হইয়া আছে এবং সম্ভবত তিনিই সেগুলির প্রতিষ্ঠা করেন। মোটের উপর মহীপালের রাজ্যে বাংলায় সকল দিকেই এক নূতন জাতীয় জাগরণের আভাস পাওয়া যায়।
মহীপালের ইমাদপুরে প্রাপ্ত লিপি তাঁহার রাজ্যের ৪৮ বৎসরে লিখিত। সুতরাং অনুমিত হয় যে তিনি প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল রাজত্ব করেন (আ ৯৮৮-১০৩৮)।
.
২. বৈদেশিক আক্রমণ ও অন্তর্বিদ্রোহ
মহীপালের পর তাঁহার পুত্র নয়পাল সিংহাসনে আরোহণ করেন ও অন্তত ১৫ বৎসর রাজত্ব করেন (আ ১০৩৮-১০৫৫)। কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেবের পুত্র কর্ণ অথবা লক্ষ্মীকর্ণের সহিত সুদীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধই তাঁহার রাজ্যকালের প্রধান ঘটনা। তিব্বতীয় গ্রন্থে এই যুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। কর্ণ মগদ আক্রমণ করিয়া নয়পালকে পরাজিত করেন। তিনি পাল-রাজধানী অধিকার করিতে পারেন নাই, কিন্তু অনেক বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করিয়া মন্দিরের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করেন। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ আচাৰ্য্য অতীশ অথবা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তখন মগধে বাস করিতেছিলেন। তিনি প্রথমে কোনো প্রকারে এই যুদ্ধব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিন্তু পরে যখন নয়পাল কর্ণকে পরাজিত করিয়া কলচুরিসৈন্য বিধ্বস্ত করিতেছিলেন তখন দীপঙ্কর কর্ণ ও তাঁহার সৈন্যকে আশ্রয় দেন। তাঁহার চেষ্টায় উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়।
কিন্তু এই সন্ধি দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। নয়পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালে (আ ১০৫৫-১০৭০) কর্ণ পুনরায় বাংলা দেশে যুদ্ধাভিযান করেন। এই যুদ্ধেও কর্ণ প্রথমে জয়লাভ করেন। বীরভূম জিলার অন্তর্গত পাইকোর নামক স্থানে একটি শিলাস্তম্ভের গাত্রে কর্ণের একখানি লিপি উত্তীর্ণ আছে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি পশ্চিমবঙ্গের কতক অংশ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তিনি তৃতীয় বিগ্রহপাল কর্ত্তৃক পরাজিত হন। তৃতীয় বিগ্রহপালের সহিত কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রীর বিবাহ হয়। সম্ভবত এই বৈবাহিক সম্বন্ধ দ্বারা উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়।
এই সুদীর্ঘ যুদ্ধের ফলে পালরাজশক্তি ক্রমশই দুর্বল হইয়া পড়ে। ফলে বাংলার নানা প্রদেশে স্বাধীন খণ্ডরাজ্যের উদ্ভব হয়। মহামাণ্ডলিক ঈশ্বরঘোষ ঢেক্করীতে রাজধানী স্থাপিত করিয়া একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। ঢেক্করী সম্ভবত বর্দ্ধমান জিলায় অবস্থিত। পূর্ব্ববঙ্গে দুইটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। বৰ্ম্মবংশীয় রাজগণ বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপিত করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের কতকাংশ শাসন করেন। কুমিল্লা অঞ্চলে পট্টিকের নামে আর একটি রাজ্য স্থাপিত হয়। কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী পট্টিকের পরগণা এখনো এই প্রাচীন রাজ্যের স্মৃতিরক্ষা করিয়াছে। এই দুই রাজ্য সম্বন্ধে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।
পালরাজগণের এই আভ্যন্তরিক দুরবস্থার সময় কর্ণাটের চালুক্যরাজগণ বাংলা দেশ আক্রমণ করেন। চালুক্যরাজ সোমেশ্বরের পুত্র কুমার বিক্রমাদিত্য দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া গৌড় ও কামরূপ জয় করেন। এতদ্ব্যতীত চালুক্যগণ একাধিকবার বঙ্গ আক্রমণ করেন।
সুযোগ পাইয়া উড়িষ্যার রাজগণও বাংলা আক্রমণ করেন। সোমবংশীয় রাজা মহাশিবগুপ্ত যযাতি গৌড় ও রাঢ়ায় জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং রাজা উদ্যোতকেশরী গৌড়ীয় সৈন্যকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ইহাদের কাহারও তারিখ সঠিক জানা যায় না। কিন্তু খুব সম্ভবত উভয়েই একাদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন।
কেবল ব্লাংলায় নহে মগধেও পালরাজশক্তি ক্রমশ হীনবল হইয়া পড়িল। নয়পালের রাজ্যকালেই গয়ার চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগে শূদ্রক নামক একজন
সেনানায়ক একটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। শূদ্রক ও তাঁহার পুত্র বিশ্বাদিত্য নামত পালরাজগণের অধীনতা স্বীকার করিতেন। কিন্তু বিশ্বাদিত্যের (নামান্তর বিশ্বরূপ) পুত্র যক্ষপাল স্বাধীন রাজার ন্যায় রাজত্ব করেন।
এইরূপ দেখা যায় যে তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যুকালে পালরাজ্য বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণে ও অন্তর্বিপ্লবে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। তৃতীয় বিগ্রহপালের তিন পুত্র ছিল-দ্বিতীয় মহীপাল, দ্বিতীয় শূরপাল ও রামপাল। দ্বিতীয় মহীপাল পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। কিন্তু চারিদিকেই তখন বিশৃঙ্খলা ও ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। দুষ্ট লোকের কথায় রাজার বিশ্বাস হইল যে তাঁহার দুই ভ্রাতা এই সমুদয় ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছেন। সুতরাং তিনি তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিলেন। কিন্তু শীঘ্রই বরেন্দ্রের সামন্তবর্গ প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইয়া রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। মহীপালের সৈন্য বা যুদ্ধসজ্জা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না কিন্তু মন্ত্রীগণের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি বিদ্রোহীগণের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। মহীপাল পরাস্ত ও নিহত হইলেন। কৈবৰ্ত্তজাতীয় নায়ক দিব্য বরেন্দ্রের রাজা হইলেন।
সন্ধ্যাকরনন্দী বিরচিত রামচরিত কাব্যে এই বিদ্রোহ ও তাঁহার পরবর্ত্তী ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। বাংলার ইতিহাসে এই গ্রন্থখানি অমূল্য-কারণ বাংলার আর কোনো রাজনৈতিক ঘটনার এরূপ বিস্তৃত বিবরণ আমরা কোথাও পাই না। সন্ধ্যাকরনন্দীর পিতা এই সমুদয় ঘটনার কালে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং তিনি নিজেও ইহার অধিকাংশ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সুতরাং সমুদয় ঘটনা যথাযথভাবে জানিবার তাঁহার বিশেষ সুযোগ ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই কাব্যখানির সম্যক অর্থ গ্রহণ করা অতিশয় কঠিন। ইহার প্রধান কারণ এই যে কাব্যখানি দ্ব্যর্থবোধক। ইহার প্রতি শ্লোকের দুই প্রকার অর্থ আছে। এক অর্থে ধরিলে কাব্যখানিতে রামায়ণে বর্ণিত রামচন্দ্রের আখ্যান এবং অন্য অর্থে পালরাজগণের, প্রধানত রামপালের, ইতিহাস পাওয়া যায়। দ্বিবিধ অর্থব্যঞ্জনার জন্য শ্লোকগুলির শব্দযোজনা এমনভাবে করিতে হইয়াছে যে সহজে তাহা বিশ্লেষণ করা যায় না। এই জন্যই কবির জীবিতকালেই, অথবা তাঁহার অল্পদিন পরেই, এই কাব্যের একটি টীকা রচিত হয়। তাহাতে দুইপক্ষের অন্বয় ও ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে এই কাব্যের যে একমাত্র পুঁথি আবিষ্কার করেন তাহাতে সম্পূর্ণ মূল গ্রন্থ ও টীকার এক অংশমাত্র পাওয়া যায়। যে অংশের শ্লোকের প্রকৃত ব্যাখ্যা, বিশেষত তাঁহার মধ্যে ঐতিহাসিক ঘটনার যে সমুদয় ইঙ্গিত বা অভ্যাস আছে তাঁহার মর্ম গ্রহণ করা সৰ্ব্বত্র সম্ভবপর হয় নাই। মূল টীকার সাহায্যে মূল গ্রন্থ হইতে বরেন্দ্রের বিদ্রোহ ও রামপাল কর্ত্তৃক বরেন্দ্রের পুনরাধিকার সম্বন্ধে যাহা জানা যায় পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইবে।
০৯. তৃতীয় পালসাম্রাজ্য
নবম পরিচ্ছেদ –তৃতীয় পালসাম্রাজ্য
১. বরেন্দ্র-বিদ্রোহ
যে বিদ্রোহের ফলে দ্বিতীয় মহীপালরাজ্য ও প্রাণ হারাইলেন কৈবর্ত্তনায়ক দিব্যের সাহিত তাঁহার কোনো সম্বন্ধ ছিল কি না তাহা নির্ণয় করা কঠিন। রামচরিতের একটি শ্লোকে এরূপ ইঙ্গিত আছে যে দিব্য মহীপালের অধীনে উচ্চরাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। রামচরিতে ইহাও স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে যে দিব্য মহীপালকে হত্যা করিয়া বরেন্দ্রভূমি অধিকার করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যে দিব্যি এই বিদ্রোহের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন ইহা অনুমান করা স্বাভাবিক। কিন্তু দিব্যের সহিত বিদ্রোহীদের কোনো প্রকার যোগাযোগ ছিল এরূপ কোনো কথা রামচরিতে নাই। সুতরাং অসম্ভব নহে যে দিব্য প্রথমে মহীপালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে যোগদান করেন নাই কিন্তু বিদ্রোহীদের হস্তে পরাজয়ের পর মহীপালকে হত্যা করিয়া তিনি বরেন্দ্রী অধিকার করিয়াছিলেন। রামচরিতে দিব্যকে দস্যু ও ‘উপব্ৰিতী’ বলা হইয়াছে টীকাকার উপব্ৰিতীর অর্থ করিয়াছেন ‘ছদ্মব্ৰিতী’। কেহ কেহ ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে দিব্য কর্তব্যবশে বিদ্রোহী সাজিয়া মহীপালকে হত্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ অর্থ সঙ্গত মনে হয় না। দস্যু ও উপব্ৰিতী হইতে বরং ইহাই মনে হয় যে রামচরিতকারের মতে দিব্য প্রকৃতই দস্যু ছিলেন, কিন্তু দেশহিতের ভান করিয়া রাজাকে হত্যা করিয়াছিলেন। বস্তুত রামচরিত কাব্যের অন্যত্রও দিব্যের আচরণ কুৎসিত ও নিন্দনীয় বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিছুদিন পর্য্যন্ত বাংলার একদল লোক বিশ্বাস করিতেন যে দিব্য অত্যাচারী মহীপালকে বধ করিয়া দেশরক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার এই মহৎ কার্যের জন্য জনসাধারণ কর্ত্তৃক রাজা নিৰ্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা দিব্যকে মহাপুরুষ সাজাইয়া উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে প্রতি বৎসর “দিব্য-স্মৃতি উৎসবের ব্যবস্থা করিতেন। কিন্তু রামচরিতে ইহার কোনো সমর্থনই পাওয়া যায় না। অবশ্য পালরাজগণের কর্ম্মচারী সন্ধ্যাকরনন্দী দিব্য সম্বন্ধে বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিবেন ইহা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু রামচরিত ব্যতীত দিব্য সম্বন্ধে জানিবার আর কোনো উপায় নাই। সুতরাং রামচরিতকার তাঁহার চরিত্রে যে কলঙ্ক লেপন করিয়াছেন তাহা পুরোপুরি সত্য বলিয়া গ্রহণ না করিলেও দিব্যকে দেশের ত্রাণকর্ত্তা মহাপুরুষ মনে করিবার কোনোই কারণ নাই।
দিব্য নিষ্কণ্টকে বরেন্দ্রের রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই। পূর্ব্ববঙ্গের বৰ্ম্মবংশীয় রাজা জাতবর্ম্মা তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন; কিন্তু এই বিরোধের হেতু বা বিশেষ কোনো বিবরণ জানা যায় না। রামপাল বরেন্দ্র উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু পারেন নাই-বরং দিব্য রামপালের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিলেন। যদিও রামচরিতে দিব্যের রাজ্যকালের কোনো ঘটনার উল্লেখ নাই, তথাপি যিনি জাতবর্ম্মা ও রামপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বরেন্দ্রী রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন তিনি যে বেশ শক্তিশালী রাজা ছিলেন এবং বরেন্দ্রে তাঁহার প্রভুত্ব বেশ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। দিব্যের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা রুদোক এবং তৎপরে রুদোকের পুত্র ভীম বরেন্দ্রর সিংহাসনে আরোহণ করেন। রামচরিতে ভীমের প্রশংসাসূচক কয়েকটি শ্লোক আছে এবং তাঁহার রাজ্যের শক্তি ও সমৃদ্ধির বর্ণনা আছে। সুতরাং দিব্য স্বীয় প্রভু ও রাজাকে বধ করিয়া যে মহাপাতক করিয়াছিলেন বরেন্দ্রে একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠাপূৰ্ব্বক তথায় সুখ-শান্তি ফিরাইয়া আনিয়া তাঁহার কতক প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। দিনাজপুরের কৈবর্ত্তস্তম্ভ (চিত্র নং ১ক) আজিও রাজবংশের স্মৃতি বহন করিতেছে।
.
২. রামপাল
দ্বিতীয় মহীপাল যখন বিদ্রোহ দমন করিতে অগ্রসর হন তখন তাঁহার দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা শূরপাল ও রামপাল কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মহীপালের পরাজয় ও মৃত্যুর পর তাঁহারা কিরূপে মুক্তি লাভ করিয়া বরেন্দ্র হইতে পলায়ন করেন রামচরিতে তাঁহার কোনো উল্লেখ নাই। পলায়ন করিবার পর পালরাজ্যের কোনো এক অংশে, সম্ভবত মগধে, শূরপাল রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজ্যকালের কোনো বিবরণই জানা যায় নাই। সম্ভবত তিনি খুব অল্পকালই রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তারপর রামপাল রাজা হন।
রামপাল রাজা হইয়া বরেন্দ্র উদ্ধার করিবার প্রয়াস করিয়াছিলেন কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া বহুদিন নিশ্চেষ্ট ছিলেন। তারপর আবার এক গুরুতর বিপদ উপস্থিত হইলে পুত্র ও অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া বিপুল উদ্যমে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। এই গুরুতর বিপদ কী, রামচরিতকার তাঁহার উল্লেখ করেন নাই। সম্ভবত দিব্য কর্ত্তৃক আক্রমণই এই বিপদ এবং রাজ্যের অবশিষ্ট অংশ হারাইবার ভয়েই বিচলিত হইয়া রামপাল পুনরায় দিব্যের প্রতিরোধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।
দিব্যের বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহের জন্য রামপাল সামন্তরাজগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিলেন। অর্থ ও সম্পত্তির প্রলোভনে অনেকেই তাঁহাকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইল। এইরূপে বহুদিনের চেষ্টায় রামপাল অবশেষে বিপুল এক সৈন্যদল সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলেন।
রামপালের প্রধান সহায় ছিলেন তাঁহার মাতুল রাষ্ট্রকূটকুলতিলক মথন। ইনি মহন নামেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি দুই পুত্র মহামাগুলিক কাহুরদেব ও সুবর্ণদেব এবং ভ্রাতৃম্পুত্র মহাপ্রতীহার শিবরাজ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া আসিলেন। অপর যে সমুদয় সামন্তরাজ রামপালকে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম রামচরিতে পাওয়া যায়। রামচরিতের টীকায় ইহাদের রাজ্যের নামও দেওয়া আছে কিন্তু তাঁহার অনেকগুলির অবস্থান নির্ণয় করা যায় না।
১। ভীমযশ-ইনি মগধ ও পীঠীর অধিপতি ছিলেন এবং কান্যকুব্জরাজের সৈন্য পরাস্ত করিয়াছিলেন।
২। কোটাটবীর রাজা বীরগুণ।
৩। দণ্ডভুক্তির রাজা জয়সিংহ। দণ্ডভুক্তির মেদিনীপুর জিলায় অবস্থিত ছিল।
৪। দেবগ্রামের রাজা বিক্রমরাজ।
৫। অরণ্য প্রদেশস্থ সামন্তবর্গের চূড়ামণি অপরমারের (হুগলী জিলান্তৰ্গত) অধিপতি লক্ষ্মীশূর।
৬। কুজবটীর (সাঁওতাল পরগণা) রাজা শূরপাল।
৭। তৈলকম্পের (মানভূম) রাজা রুদ্রশিখর।
৮। উচ্ছলের রাজা ভাস্কর অথবা ময়গলসিংহ।
৯। ঢেক্করীরাজ প্রতাহসিংহ।
১০। (বর্ত্তমান রাজমহলের নিকটবর্ত্তী) কয়ঙ্গলমণ্ডলের অধিপতি নরসিংহাৰ্জ্জুন।
১১। সঙ্কট গ্রামের রাজা চণ্ডাৰ্জ্জুন।
১২। নিদ্রাবলীর রাজা বিজয়রাজ।
১৩। কৌশাম্বীর রাজা দ্বোরপবর্দ্ধন। কৌমাঘী সম্ভবত রাজসাহী অথবা বগুড়া জিলায় অবস্থিত ছিল।
১৪। পদুবহুবার রাজা সোম।
এই সমুদয় ব্যতীত আরও অনেক সামন্তরাজ রামপালের সহিত যোগ দিয়াছিলেন-রামচরিতে তাঁহাদের সাধারণভাবে উল্লেখ আছে, নাম দেওয়া নাই। ইহার মধ্যে যে সমুদয় সামন্তরাজ্যের অবস্থিতি মোটামুটি জানা যায় তাঁহার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে প্রধানত মগধ ও রাঢ়দেশের সামন্তগণই রামপালের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন।
রামপাল সম্ভবত দক্ষিণবঙ্গ হইতে বরেন্দ্র আক্রমণ করেন। সমস্ত সামন্ত রাজগণের সৈন্য একত্রিত করিয়া তিনি প্রথমে মহাপ্রতীহার শিবরাজকে একদল সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। এই সৈন্যদল গঙ্গা নদী পার হইয়া বরেন্দ্রভূমি বিধ্বস্ত করে। এইরূপে গঙ্গার অপর তীর সুরক্ষিত করিয়া রামপাল তাঁহার বিপুল সৈন্যদল লইয়া বরেন্দ্রভূমি আক্রমণ করেন। এইবার কৈবৰ্তরাজ ভীম সসৈন্যে রামপালকে বাধা দিলেন এবং দুই দলে ভীষণ যুদ্ধ হইল। রামচরিতে নয়টি শ্লোকে এই যুদ্ধের বর্ণনা আছে। রামপাল ও ভীম উভয়ই বিশেষ বিক্রম প্রদর্শন করেন এবং পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করেন। কিন্তু হস্তীপৃষ্ঠে যুদ্ধ করিতে করিতে দৈববিড়ম্বনায় ভীম বন্দী হইলেন। ইহাতে তাঁহার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। যদিও হরি নামক তাঁহার এক সুহৃদ পুনরায় তাঁহার সৈন্যগণকে একত্র করিয়া যুদ্ধ করেন এবং প্রথমে কিছু সফলতাও লাভ করেন, তথাপি পরিশেষে রাজপালেরই জয় হইল। রামপাল ভীমের কঠোর দণ্ড বিধান করিলেন। ভীমকে বধ্যভূমিতে নিয়া প্রথমেই তাঁহার সম্মুখেই তাঁহার পরিজনবর্গকে হত্যা করা হইল। তারপর বহু শরাঘাতে ভীমকেও বধ করা হইল। এইরূপে কৈবৰ্ত্তনায়কের বিদ্রোহ ও ভীমের জীবন অবসান হইল।
বহুদিন পরে রামপাল আবার পিতৃভূমি বরেন্দ্রী ফিরিয়া পাইয়া প্রথমে ইহার শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে যত্নবান হইলেন। তিনি প্রজার করভার লাঘব এবং কৃষির উন্নতি বিধান করিলেন। তারপর রামাবতী নামক নতুন এক রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই রামাবতী নগরী সম্ভবত মালদহের নিকটবর্ত্তী ছিল।
এইরূপে পিতৃভূমি বরেন্দ্ৰীতে স্বীয় শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রামপাল নিকটবর্ত্তী রাজ্যসমূহ জয় করিয়া পালসাম্রাজ্যের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিতে যত্নবান হইলেন।
বিক্রমপুরের বৰ্ম্মরাজ সম্ভবত বিনা যুদ্ধেই রামপালের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। রামচরিতে উক্ত হইয়াছে যে পূৰ্ব্বদেশীয় বৰ্ম্মরাজ নিজের পরিত্রাণের জন্য উৎকৃষ্ট হস্তী রথ উপঢৌকন দিয়া রামপালের আরাধনা করিলেন।
কামরূপ যুদ্ধে বিজিত হইয়া অধীনতা স্বীকার করিল। সম্ভবত রামপালের কোনো সামন্ত রাজা এই যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন। তিনি কামরূপ জয় করিয়া ফিরিয়া আসিলে রামপাল তাঁহাকে বহু সম্মানদানে আপ্যায়িত করিলেন।
এইরূপে পূৰ্ব্বদিকের সীমান্ত প্রদেশ জয় করিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইলেন। রাদেশের সামন্তগণ সকলেই রামপালের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সাহায্যে রামপাল উড়িষ্যা অধিকার করিলেন। এই সময় উড়িষ্যার রাজনৈতিক অবস্থা বিশেষ শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। দক্ষিণ হইতে গঙ্গারাজগণ পুনঃপুন আক্রমণ করিয়া ইহাকে বিপর্যস্ত করিতেছিলেন। রামপালের সামন্তরাজ দণ্ডভুক্তির অধিপতি জয়সিংহ রামপালের বরেন্দ্র অভিযানে যোগ দিবার পূর্ব্বেই উৎকলরাজ কর্ণকেশরীকে পরাজিত করিয়াছিলেন। গঙ্গারাজগণ উৎকল অধিকার করিলে বাংলা দেশেরসমূহ বিপদ এই আশঙ্কায়ই সম্ভবত রামপাল নিজের মনোনীত একজনকে উৎকলের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ঠিক অনুরূপ কারণেই অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ রাজ্যচ্যুত উৎকলরাজকে আশ্রয় দিলেন। এইরূপে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার রক্ষকরূপে উৎকলের অধিকার লইয়া রামপাল ও অনন্তবর্ম্মার মধ্যে বহুদিনব্যাপী যুদ্ধ চালিয়াছিল। রামচরিত অনুসারে রামপাল উত্তাল জয় করিয়া কলিঙ্গদেশ পৰ্য্যন্ত স্বীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। অনন্তবর্ম্মার লিপি হইতে জানা যায় যে ১১৩৫ অব্দের অনতিকাল পূর্ব্বে তিনি উড়িষ্যা জয় করিয়া স্বীয় রাজ্যভুক্ত করেন। সুতরাং রামপালের মৃত্যু পর্য্যন্ত উড়িষ্যায় তাঁহার আধিপত্য ছিল ইহা অনুমান করা যাইতে পারে।
রামচরিতের একটি শ্লোকে একপক্ষে সীতার সৌন্দর্য ও অপরপক্ষে বরেন্দ্রীর সহিত অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক সম্বন্ধ বর্ণিত হইয়াছে। টীকা না থাকায় এই শ্লোকের সমুদয় ইঙ্গিত স্পষ্ট বোঝা যায় না, কিন্তু কয়েকটি সিদ্ধান্ত বেশ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। প্রথমত রামপাল অঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন (অবনমদঙ্গা) দ্বিতীয়ত তিনি কর্ণাটরাজগণের লোলুপ দৃষ্টি হইতে বঙ্গদেশকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (অধরিতকর্ণাটেক্ষণলীলা)। তৃতীয়ত তিনি মধ্যদেশের রাজ্যবিস্তারে বাধা দিয়াছিলেন (ধৃতমধ্যদেশতনিমা)।
অঙ্গ ও মগধ যে রামপালের রাজ্যভুক্ত ছিল শিলালিপি হইতে তাঁহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কর্ণাটদেশীয় চালুক্যরাজগণের বাংলা আক্রমণের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রামপালের রাজ্যকালে আৰ্য্যাবৰ্তে কৰ্ণাটগণের প্রভুত্ব আরও বিস্তার লাভ করে। কর্ণাটের দুইজন সেনানায়ক পালসাম্রাজ্যের সীমার মধ্যেই দুইটি রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমটি রাঢ়দেশের সেনরাজ্য। রামপালের জীবিতকালে ইহা খুব শক্তিশালী ছিল না, এ বিষয়ে পরে আলোচিত হইবে। কিন্তু কর্ণাটবীর নান্যদেব একাদশ শতাব্দের শেষভাগে (আ ১০৯৭) মিথিলায় আর একটি প্রবল স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। মিথিলা প্রথম মহীপালের সময় পালরাজ্যভুক্ত ছিল। নান্যদেবের সহিত গৌড়াধিপের সংঘর্ষ হয়। এই গৌড়াধিপ সম্ভবত রামপাল, কারণ রামপালকে পরাজিত না করিয়া কোনো কর্ণাটবীর মিথিলায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন ইহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং কর্ণাটের লোলুপ দৃষ্টি এ সময় বাংলার বিশেষ আশঙ্কা ও উদ্বেগের কারণ হইয়াছিল। রামপালের জীবিতকালে নান্য বাংলা জয় করিতে পারেন নাই এবং সেনরাজগণও মাথা তুলিতে পারেন নাই-সম্ভবত রামচরিতকার ইহাই ইঙ্গিত করিয়াছেন। রামপালের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই কর্ণাটদেশীয় সেনরাজগণ সমস্ত বাংলা দেশ জয় করেন। সুতরাং রামপাল যে কর্ণাটের লোলুপ দৃষ্টি হইতে বাংলা দেশ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন ইহা কম কৃতিত্বের কথা নহে।
রামপালের রাজ্যকালে গাহড়বালবংশীয় চন্দ্রদেবের বর্ত্তমান যুক্তপ্রদেশে একটি শক্তিশালী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। কাশী ও কান্যকুব্জ এই রাজ্যের দুইটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। পালরাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত থাকায় পালরাজগণের সহিত ইহাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। গাহড়বালরাজগণের লিপি হইতে জানা যায় যে, ১১০৯ অব্দের পূৰ্ব্বে গাহড়বালরাজ মদনপালের পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের সহিত গৌড়রাজের যুদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধে যে গোবিন্দচন্দ্র জয়লাভ করিয়া গৌড়রাজ্যের কোনো অংশ অধিকার করিয়াছিলেন তাঁহার প্রশস্তিকারও এমন কথা বলেন নাই। সুতরাং রামপাল মধ্যদেশের রাজ্যবিস্তার প্রতিরোধ করিতে পারিয়াছিলেন রামচরিতের এই উক্তি বিশ্বাসযোগ্য বলিয়াই মনে হয়। এই প্রসঙ্গে ইহাই উল্লেখযোগ্য যে গোবিন্দচন্দ্রের রাণী কুমারদেবী রামপালের মাতুল মহণের দৌহিত্রী ছিলেন। অসম্ভব নহে যে মহণ এই বৈবাহিক সম্বন্ধ দ্বারা রামপালের সহিত গাহড়বালরাজের মিত্রতা স্থাপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং কতক পরিমাণে কৃতকাৰ্যও হইয়াছিলেন। মহণ যে কেবল রামপালের মাতুল ছিলেন এবং তাঁহার ঘোর বিপদের দিনে পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রসহ তাঁহার সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা নহে, উভয়ে অভিন্নহৃদয় সুহৃৎ ছিলেন। বৃদ্ধবয়সে রামপাল মহণের মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া এত শোকাকুল হইলেন যে নিজের প্রাণ বিসর্জন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। মুগগিরি (মুঙ্গের) নগরীতে গঙ্গাগর্ভে প্রবেশপূৰ্ব্বক তিনি এই নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া স্বর্গে মাতুলের সহিত মিলিত হইলেন। বন্ধুর শোকে এইরূপ আত্মবিসর্জনের দৃষ্টান্ত জগতে বিরল।
রামপাল ৪২ বৎসরেরও অধিককাল রাজ্য করেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহীপালের রাজ্যকালেই তিনি যৌবনে পদার্পণ করেন, অন্যথা তিনি সিংহাসনের জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছেন এরূপ অপবাদ বিশ্বাসযোগ্য হইত না। সুতরাং মৃত্যুকালে তাঁহার অন্ত ত ৭০ বৎসর বয়স হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। তিনি সম্ভব ১০৭৭ হইতে ১১২০ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।
রামপালের জীবন ও মৃত্যু উভয়ই বিচিত্র। তাঁহার কাহিনী ইতিহাস অপেক্ষা উপন্যাসের অধিক উপযোগী জীবনের প্রারম্ভে জ্যেষ্ঠভ্রাতার অমূলক সন্দেহের ফলে যখন কারাগারে শৃঙ্খলিত অবস্থায় তিনি নিদারুণ শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, তখন অন্তর্বিপ্লবের ফলে বরেন্দ্রে পালরাজ্যের অবসান হইল। সেই ঘোর দুর্যোগের দিনে অসহায় বন্দী রামপাল কিরূপে জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন ইতিহাস তাঁহার কোনো সন্ধান রাখে না। তারপর পিতৃরাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া কোন নিভূত প্রদেশে তিনি দীর্ঘকাল দুঃসহ মনোব্যথায় জীবন যাপন করিয়াছিলেন তাহাও জানা যায় না। যখন বিপদ আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল এবং সম্ভবত তাঁহার শেষ আশ্রয়টুকুও হস্তচ্যুতে হইবার উপক্রম হইল, তখন ধর্ম্মপাল ও দেবপালের উত্তরাধিকারী এবং প্রথম মহীপালের বংশধর ভারতপ্রসিদ্ধ রাজবংশের এই শেষ মুকুটমণি লজ্জা ঘৃণা ভয় ত্যাগ করিয়া অধীনস্থ সামন্ত রাজগণের দ্বারে দ্বারে সাহায্য ভিক্ষা করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্যম ও অধ্যবসায়ে রাজলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইলেন। বরেন্দ্র পুনরধিকৃত হইল, বাংলা দেশের সর্বত্র তিনি প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং কামরূপ ও উৎকল জয় করিলেন। দক্ষিণ দিগ্বিজয় অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ এবং পশ্চিমে চালুক্য ও গাহড়বাল এই তিনটি প্রবল রাজশক্তির বিরুদ্ধে তাঁহাকে সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। তাঁহার বাহুবলে খণ্ড-বিখণ্ড বাংলা দেশে আবার একতা ও সুদৃঢ় রাজশক্তি ফিরিয়া আসিল, বাঙ্গালী আবার সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখিল। নিভিবার ঠিক আবেগ প্রদীপ যেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠে রামপালের রাজ্যকালে পালরাজ্যের কীৰ্তিশিখাও তেমনি শেষবারের মতো জ্বলিয়া উঠিল। রামপালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পালবংশের গৌরবরবি চিরদিনের তরে অস্তমিত হইল।
১০. পালরাজ্যের ধ্বংস
দশম পরিচ্ছেদ –পালরাজ্যের ধ্বংস
রামপালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র কুমারপাল রাজা হইলেন। রামচরিতে উক্ত হইয়াছে যে রামপালের দুই পুত্র বিত্তপাল ও রাজ্যপাল বরেন্দ্রের বিদ্রোহ দমনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। রামপালের আর এক পুত্র মদনপাল পরে পালরাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন। রামপালের এই চারি পুত্রের মধ্যে কে সৰ্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন, এবং কোন অধিকারে কুমারপাল পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনের আরোহণ করিয়াছিলেন তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই।
কুমারপালের রাজত্বকালে (আ ১১২০-১১২৫) দক্ষিণবঙ্গে বিদ্রোহ হইয়াছিল এবং তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর বন্ধু প্রধান অমাত্য” বৈদ্যদেব নৌযুদ্ধে বিদ্রোহীগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই পূৰ্ব্বভাগে, সম্ভবত কামরূপে, তিগ্যদেব বিদ্রোহী হইয়াছিলেন এবং বৈদ্যদেব তাঁহাকে পরাজিত করিয়া সেই রাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে, সম্ভবত কুমারপালের মৃত্যুর পর, বৈদ্যদেব কামরূপে স্বাধীনভাবে রাজ্য করেন। কুমারপালের পর তাঁহার পুত্র তৃতীয় গোপাল রাজা হন। তাঁহার রাজত্বকালের (আ ১১২৫-১১৪০) কোনো ঘটনাই জানা যায় না। কিন্তু পালরাজ্যের অন্তর্বিদ্রোহ সম্ভবত এই সময় আরও বিস্তৃত হয়। পূর্ব্ববঙ্গে বৰ্মণ রাজারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সুযোগ পাইয়া দক্ষিণ হইতে গঙ্গরাজগণ পালরাজ্য আক্রমণ করেন। ১১৩৫ অব্দের পূর্ব্বে অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ মেদিনীপুর ও হুগলী জিলার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হইয়া গঙ্গাতীরবর্ত্তী মন্দার প্রদেশ পর্য্যন্ত জয় করেন। তিনি যে মিথুনপুর ও আরম্য দুর্গ অধিকার করেন তাহা সম্ভবত আধুনিক মেদিনীপুর ও আরামবাগ (হুগলী জিলা)। দাক্ষিণাত্যের চালুক্য রাজগণও পশ্চিমবঙ্গ আক্রমণ করেন এবং ইহার ফলে রাদেশের সেনরাজবংশ প্রবল হইয়া ওঠে। গাহড়বাল রাজগণও মগধ আক্রমণ করিয়া পাটনা পৰ্য্যন্ত অধিকার করেন।
তৃতীয় গোপালের মৃত্যুর পর মদনপাল যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন এইরূপে আভ্যন্তরিক বিদ্রোহ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে পালরাজ্য দ্রুতবেগে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছিল। মদনপাল চতুর্দিকে শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া পালরাজ্য রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন কিন্তু সমর্থ হইলেন না। রামচরিতের একটি শ্লোক হইতে অনুমিত হয় যে তিনি অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গের সহিত যুদ্ধে কিছু সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময়ে গাহড়বালগণ আরও অগ্রসর হইয়া মুঙ্গের নগরী পৰ্য্যন্ত অধিকার করে। অনেক চেষ্টার পরও মদনপাল এই অঞ্চল শহস্ত হইতে পুনরুদ্ধার করেন। কিন্তু শ্রীঘই তাঁহাকে অন্যান্য শক্রর বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে হয়। গোবর্দ্ধন নামক এক রাজাকে তিনি পরাজিত করেন। সম্ভবত ইনি বাংলার কোনো অঞ্চলে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। আর এক প্রবল শক্র মদনপালের বহু সৈন্য নষ্ট করিয়াছিল। মদনপাল বহু কষ্টে তাহাকে কালিন্দী নদীর তীর পর্য্যন্ত হঠাইয়া দেন। এই নদী সম্ভবত মালদহের নিকটবর্ত্তী কালিন্দী নদী। এইরূপে যে শক্ররাজা গৌড় দেশের একাংশ জয় করিয়া প্রায় পালরাজধানী পৰ্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন তিনি সম্ভবত সেনরাজ বিজয় সেন। বিজয় সেনের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, তিনি গৌড়রাজকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন এবং গৌড়রাজ্যের অন্তত কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন। এই পরাজিত গৌড়রাজ যে মদনপাল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। মদনপাল আনুমানিক ১১৪০ হইতে ১১৫৫ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।
মদনপালের রাজত্বের সমুদয় ঘটনার বিশদ বিবরণ অথবা পারম্পর্য সঠিক না জানিতে পারিলেও ইহা অনায়াসেই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে তাঁহার মৃত্যুকালে দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গে তাঁহার কোনো অধিকারই ছিল না। উত্তরবঙ্গেরও সমগ্র অথবা অধিকাংশ তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল। সুতরাং পালরাজ্য এই সময়ে মগধের মধ্যে ও পূৰ্ব্বভাগে সীমাবদ্ধ ছিল।
মদনপালের পর গোবিন্দপাল নামে এক রাজা গয়ায় রাজত্ব করেন। ইহারও পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি পদবী এবং গৌড়েশ্বর উপাধি ছিল। সম্ভবত মদনপালের মৃত্যুর পরই তিনি রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ১১৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট হয়। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন এবং একখানি বৌদ্ধ পুঁথিতে ‘শ্রীমদগোবিন্দপালদেবানাং বিনষ্টরাজ্যে অষ্টত্রিংশৎ সম্বৎসরে’ এইরূপ কালজ্ঞাপন পদ পাওয়া যায়। অপর কয়েকখানি পুঁথিতে বিনষ্টরাজ্যের পরিবর্তে ‘গতরাজ্যে’, ‘অতীত-সম্বৎসর’ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সমুদয় কালজ্ঞাপক বাক্য হইতে অনুমিত হয় যে গোবিন্দপালই মগধে শেষ বৌদ্ধ রাজা, এবং এইজন্যই বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ তাঁহার মৃত্যুর পর বিধর্মী রাজার প্রবর্দ্ধমান বিজয়রাজ্যের উল্লেখ না করিয়া গোবিন্দপালের রাজ্য-ধ্বংস হইতে কাল গণনা করিতেন।
গোবিন্দপাল পালরাজবংশীয় ছিলেন কি না তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। তাঁহার পদবী ও উপাধি, বৌদ্ধধৰ্ম্ম, ও মদনপালের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই মগধে রাজত্বের কথা বিবেচনা করিলে তিনি যে পালরাজবংশীয় ছিলেন এরূপ অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও মদনপালের সহিত তাঁহার কী সম্বন্ধ ছিল, এবং গয়ার বাহিরে তাঁহার রাজ্য কত দূর বিস্তৃত ছিল–অর্থাৎ তাঁহার গৌড়েশ্বর উপাধি কেবলমাত্র পূৰ্বগৌরবের সূচক অথবা গৌড়রাজ্যে তাঁহার কোনোকালে কোনো প্রকার অধিকার ছিল-ইত্যাদির বিষয়ে কিছুই বলা যায় না। তবে ইহা এক প্রকার স্থির সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ১১৬২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ধর্ম্মপাল, দেবপাল, মহীপাল ও রামপালের স্মৃতিবিজড়িত পালরাজ্যের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যায়।
কেহ কেহ পলপাল, ইন্দ্রদ্যুম্নপাল প্রভৃতি দুই-একজন পরবর্ত্তী পাল উপাধিধারী রাজার উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইঁহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।
১১. বৰ্ম্মরাজবংশ
একাদশ পরিচ্ছেদ –বৰ্ম্মরাজবংশ
একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন পালরাজশক্তি ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল তখন পূর্ব্ববঙ্গে বৰ্ম্ম-উপাধিধারী এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ঢাকা জিলার অন্তর্গত বেলাব গ্রামে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসনই এই রাজবংশের ইতিহাসের প্রধান অবলম্বন। এই শাসনে বৰ্ম্মরাজগণের বংশপরিচয়ে প্রথমে পৌরাণিক কাহিনী অনুযায়ী ব্রহ্মা হইতে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে অত্রি, চন্দ্র, বুধ, পুরূরবা, আয়ু নহুষ, যযাতি ও যদুর, এবং এই যদুবংশে হরির অবতার কৃষ্ণের জন্মের উল্লেখ আছে। এই হরির বান্ধব অর্থাৎ জ্ঞাতি বৰ্ম্মবংশ বৈদিক ধর্ম্মের প্রদান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং সিংহপুরে রাজত্ব করিতেন। এই বংশীয় বজ্ৰবর্ম্মা একাধারে বীর, কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র জাতবর্ম্মা বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সার্বভৌমত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অঙ্গদেশে স্বীয় ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, কামরূপ জয় করিয়াছিলেন, দিব্যের ভুজবল হতশ্রী করিয়াছিলেন, এবং গোবর্দ্ধন নামক রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। প্রশস্তিকারের দ্ব্যর্থবোধক শ্লোকের এই উক্তি কত দূর সত্য তাহা বলা যায় না। ঐ শ্লোকে ইহাও বলা হইয়াছে যে তিনি কর্ণের কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ডাহলের কলচুরিরাজ কর্ণ যে পালরাজ্য আক্রমণ করিয়া বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং অবশেষে পালরাজ তৃতীয় বিগ্রহপালের সহিত স্বীয় কন্যা যৌবনশ্রীর বিবাহ দিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং অসম্ভব নহে যে জাতবর্ম্মা কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেব ও কর্ণের অধীনস্থ সামন্তরাজরূপে তাঁহাদের সঙ্গে পালরাজ্য আক্রমণ করেন, এবং অঙ্গদেশে পালরাজ ও বরেন্দ্রে কৈবর্ত্যরাজ দিব্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। তারপর কোনো সুযোগে পূর্ব্ববঙ্গে অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া কামরূপ আক্রমণ করেন ও গোবর্দ্ধন নামক বঙ্গদেশীয় কোনো রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। অবশ্য এ সকলই বর্ত্তমানে অনুমান মাত্র কারণ ইহার সপক্ষে বিশিষ্ট কোনো প্রমাণ নাই। কিন্তু এইরূপ কোনো অনুমানের আশ্রয় না লইলে সিংহপুর নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি জাতবৰ্ম্মা কেবলমাত্র নিজের বাহুবলে অঙ্গ, কামরূপ ও বরেন্দ্রে বিজয়াভিযান করিয়া বঙ্গে এক স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এরূপ বিশ্বাস করা কঠিন।
বৰ্ম্মরাজগণের আদিম রাজ্য সিংহপুর কোথায় ছিল এ বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। পঞ্জাবের একখানি শিলালিপিতে সিংহপুরের যাদব বংশসস্তৃতা জালন্ধরের এক রাণীর কথা আছে এবং হুয়েন সাংও পঞ্জাবে এক সিংহপুর রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহাই পূর্ব্ববঙ্গের যাদববংশীয় বৰ্ম্মরাজগণের আদি বাসভূমি। কলিঙ্গেও এক সিংহপুর রাজ্য ছিল-এই স্থান বর্ত্তমানে সিঙ্গুপুর নামে পরিচিত এবং চিকাকোল ও নরাসন্নপেতার মধ্যস্থলে অবস্থিত। সিংহলদেশীয় গ্রন্থে যে বিজয়সিংহের আখ্যান আছে তাহাতে রাঢ়দেশে এক সিংহপুরের উল্লেখ আছে; ইহা সম্ভবত হুগলী জিলার অন্তর্গত সিঙ্গুর নামক গ্রামে অবস্থিত ছিল। বৰ্মগণের আদি বাসভূমি কলিঙ্গ রাঢ়ের অন্তর্গত সিংহপুরে ছিল ইহাও কেহ কেহ অনুমান করেন। কলিঙ্গের সিংহপুর রাজ্য পঞ্চম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল ইহার বিশেষ প্রমাণ আছে। খুব সম্ভবত জাতবর্ম্মা এই রাজ্যেরই অধিপতি ছিলেন। কলচুরিরাজগণের প্রশস্তি অনুসারে গাঙ্গেয়দেব অঙ্গ ও উৎকলের রাজাকে পরাজিত করেন ও তৎপুত্র কর্ণ গৌড়, বঙ্গ ও কলিঙ্গে আধিপত্য করেন। সুতরাং কলিঙ্গদেশীয় জাতবর্ম্মা কলচুরিরাজগণের অধীনে অঙ্গ, গৌড় ও বঙ্গে যুদ্ধাভিযান করিয়াছিলেন এবং এই সুযোগে বঙ্গে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন এরূপ অনুমানই খুব স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।
বেলাব তাম্রশাসনে জাতবর্ম্মার পর তাঁহার পুত্র সামলবর্ম্মার উল্লেখ আছে। কিন্তু ঢাকার নিকটবর্ত্তী বজ্রযোগিনী গ্রামে এই সামলবর্ম্মার একখানি তাম্রশাসনের যে একটি খণ্ডমাত্র পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে অনুমিত হয় যে, জাতবর্ম্মার পরে হরিবর্ম্মা রাজত্ব করেন। এই তাম্রশাসনখানির অবশিষ্ট অংশ না পাওয়া পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কোনো স্থির সিদ্ধান্ত করা যায় না। কিন্তু হরিবৰ্ম্মা নামে যে একজন রাজা ছিলেন তাঁহার বহু প্রমাণ আছে। দুইখানি বৌদ্ধ গ্রন্থের পুঁথি মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর পরমভট্টারক হরিবর্ম্মার রাজত্বের ১৯ ও ৩৯ সংবৎসরে লিখিত হইয়াছিল। হরিবর্ম্মার মন্ত্রী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ভবদেব ভট্টের একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে; ইহাতেও হরিবৰ্ম্মার উল্লেখ আছে। হরিবর্ম্মার একখানি তাম্রশাসন সামন্তসার গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। দুঃখের বিষয় অগ্নিদগ্ধ হওয়ায় এই তাম্রশাসনখানির পাঠ অনেক স্থলেই অস্পষ্ট ও দুর্বোধ। ইহাতে হরিবৰ্ম্মার পিতার নাম আছে। নগেন্দ্রনাথ বসু ইহা জ্যোতিবর্ম্মা পড়িয়াছিলেন কিন্তু নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে ইহা সম্ভবত জাতবৰ্ম্মা। এই পাঠ সত্য হইলে বলিতে হইবে যে জাতবর্ম্মার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হরিবৰ্ম্মা রাজত্ব করেন।
হরিবর্ম্মার রাজধানী সম্ভবত বিক্রমপুরেই ছিল এবং তিনি প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীকাল যাবৎ রাজত্ব করেন। রামচরিতে উক্ত হইয়াছে যে হরি নামক একজন সেনানায়ক কৈবর্ত্যরাজ ভীমের পরাজয়ের পর রামপালের সহিত সুখ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, এবং প্রাকদেশীয় এক বৰ্ম্ম নরপতি স্বীয় পরিত্রাণের নিমিত্ত বিজয়ী রামপালের নিকট উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন। খুব সম্ভবত উক্ত হরি ও বৰ্ম্ম নরপতি এবং হরিবর্ম্মা একই ব্যক্তি। তবে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।
হরিবর্ম্মার পর তাঁহার পুত্র রাজা হইয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের কাহারও রাজ্যকালের বিশেষ কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে ইহাদের মন্ত্রী ভবদেবভট্ট একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন এবং একখানি শিলালিপি হইতে তাঁহার ও তাঁহার বংশের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বাংলা দেশের এই প্রকার কোনো প্রাচীন ব্রাহ্মণ বংশের সঠিক বিবরণ বিশেষ দুর্লভ, সুতরাং ইহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ প্রয়োজন।
রাঢ়দেশের অলঙ্কারস্বরূপ সিদ্ধল গ্রামের অধিবাসী ভবদেব নামক জনৈক ব্রাহ্মণ গৌড় রাজার নিকট হইতে হস্তিনীভট্ট গ্রাম উপহার পাইয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্রের পৌত্র আদিদেব বঙ্গরাজের বিশেষ বিশ্বাসভাজন মহামন্ত্রী, মহাপাত্র ও সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। তাঁহার পুত্র গোবর্দ্ধন শস্ত্র ও শাস্ত্রে তুল্য পারদর্শী ছিলেন এবং পণ্ডিতগণের সভায় ও যুদ্ধক্ষেত্রে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী বন্দ্যঘটীয় এক ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে ভবদেবভট্ট জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সিদ্ধান্ত, তন্ত্র, গণিত ও ফলসংহিতায় (জ্যোতিষ) পারদর্শী ছিলেন এবং হোরাশাস্ত্রে অভিনব সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রের ও স্মৃতির নূতন ব্যাখ্যা ও মীমাংসা সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এবং কবিকলা, সৰ্ব্ব আগম (বেদ), অর্থশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, অস্ত্রবেদ প্রভৃতি শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি রাজা হরিবর্ম্মাদেবের মন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁহার মন্ত্রশক্তির প্রভাবে ধর্ম্মবিজয়ী রাজা হরিবৰ্ম্মা দীর্ঘকাল রাজ্যসুখ ভোগ করিয়াছিলেন। প্রশস্তিকারের বর্ণনা অনুসারে ভবদেবভট্ট একজন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। অতিরঞ্জিত হইলেও ভবদেবের পাণ্ডিত্যের বিবরণ যে অনেকাংশে সত্য তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ তাঁহার মীমাংসা ও স্মৃতিবিষয়ক গ্রন্থ এখনো প্রচলিত ও প্রসিদ্ধ। সংস্কৃত সাহিত্য প্রসঙ্গে পরে ইহার আলোচনা করা যাইবে। ভবদেবের বালবলভীভুজঙ্গ এই উপাধি ছিল। ইহার প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করা দুরূহ। অনেকেই মনে করেন যে বালবলভী কোনো স্থানের নাম। কিন্তু ভীমসেন প্রণীত সুধাসাগরে এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে। তাহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। বলভী শব্দের অর্থ বাটীর সর্বোচ্চ কক্ষ। এইরূপ এক বলভীতে ব্রাহ্মণ বালকগণের পাঠশালা ছিল। ইহাদের মধ্যে গৌড়দেশীয় বালক ভবদেব বুদ্ধিমত্তায় ও বাচ্চাতুর্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল এবং অন্যান্য বালকগণ তাহাকে বিশেষ ভয় করিত। এই জন্য গুরুমহাশয় এই বালককে বালবলভীভুজঙ্গ এই উপাধি প্রদান করেন।
হরিবর্ম্মা ও তাঁহার পুত্রের পর জাতবর্ম্মার অপর পুত্র সামলবৰ্ম্মা রাজা হন। মহারাজাধিরাজ সামলবর্ম্মার রাজ্যকালের কোনো বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ জানা যায় না, কিন্তু বাংলার বৈদিক ব্রাহ্মণগণের কুলজী গ্রন্থ অনুসারে রাজা সামলবর্ম্মার আমন্ত্রণে তাঁহাদের পূৰ্বপুরুষ ১০০১ শকে বাংলা দেশে আগমন করেন। আবার কোনো কোনো কুলজী মতে রাজা হরিবর্ম্মাই বৈদিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। মোটের উপর বাংলায় বৈদিক ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বর্ম্মারাজবংশের সহিত জড়িত। কুলজীতে যে তারিখ (১০৭৯ অব্দ) আছে তাহা একেবারে ঠিক না হইলেও খুব বেশি ভুল বলা যায় না। কারণ জাতবর্ম্মা তৃতীয় বিগ্রহপালের সমসাময়িক, সুতরাং একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিতেন; এবং তাঁহার পুত্রদ্বয় হরিবর্ম্মা ও সামলবর্ম্মা একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমে রাজত্ব করিয়াছিলেন ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।
সামলবর্ম্মার পর তাঁহার পুত্র ভোজবর্ম্মা রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজধানী বিক্রমপুর হইতে তাঁহার রাজত্বের পঞ্চম বৎসরে বেলাব-তাম্রশাসন প্রদত্ত হয়। এই তাম্রশাসনে ভোজবর্ম্মা পরমবৈষ্ণব পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। সুতরাং তিনি যে একজন স্বাধীন ও পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। কিন্তু ভোজবর্ম্মার পরে এই বংশের কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। সম্ভবত দ্বাদশ শতাব্দের প্রথমার্ধে সেনরাজবংশীয় বিজয়সেন এই বৰ্ম্মরাজবংশের উচ্ছেদ করেন।
১২. সেনরাজবংশ
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ –সেনরাজবংশ
১. উৎপত্তি
সেনরাজগণের পূর্ব্বপুরুষগণ দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কর্ণাটদেশের অধিবাসী ছিলেন। বম্বে প্রদেশ ও হায়দ্রাবাদ রাজ্যের দক্ষিণ এবং মহীশূর রাজ্যের উত্তর ও পশ্চিম ভাগ প্রাচীন কর্ণাটদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেনরাজগণের শিলালিপি অনুসারে তাঁহারা চন্দ্রবংশীয় এবং ব্রহ্মক্ষত্রিয় ছিলেন। বাংলা দেশের প্রাচীন কুলজী গ্রন্থে তাঁহাদিগকে বৈদ্য জাতীয় বলা হইয়াছে। আধুনিককালে তাহাদিগকে কায়স্থ এবং বাংলা দেশের অন্যান্য সুপরিচিত জাতিভুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু এ বিষয়ে সমসাময়িক লিপিতে তাঁহাদের নিজেদের উক্তি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং সেনরাজগণ যে জাতিতে ব্রহ্মক্ষত্রিয় ছিলেন সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই। বাংলা দেশে আসিবার পর তাহারা হয়ত বৈবাহিক সম্বন্ধ দ্বারা বৈদ্য অথবা অন্য কোনো জাতির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।
ব্ৰহ্মক্ষত্রিয় একটি সুপরিচিত জাতি। অনেকে মনে করেন যে প্রথমে ব্রাহ্মণ ও পরে ক্ষত্রিয় হওয়াতেই এই জাতির এরূপ নামকরণ হইয়াছে। সেনরাজগণের এক পূৰ্বপুরুষ ব্রহ্মবাদী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। এই সময় কর্ণাটদেশে (বর্ত্তমান ধারবাড় জিলায়) সেন উপাধিধারী অনেক জৈন আচার্যের নাম পাওয়া যায়। ইঁহারা সেনবংশীয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে বাংলার সেনরাজগণ এই জৈন আশ্চার্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তাঁহারা জৈনধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শৈবধর্ম্ম ও পরবর্ত্তীকালে ধৰ্ম্মচৰ্য্যার পরিবর্তে শস্ত্ৰচৰ্য্যা গ্রহণ করেন। এই অনুমান কত দূর সত্য তাহা বলা কঠিন।
সেনরাজগণ কোন সময়ে বাংলা দেশে প্রথম বসতি স্থাপন করেন সে সম্বন্ধে সেনরাজগণের লিপিতে যে দুইটি উক্তি আছে তাহা প্রথমে পরস্পরবিরোধী বলিয়াই মনে হয়। বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপিতে কথিত হইয়াছে যে সামন্তসেন রামেশ্বর সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত বহু যুদ্ধাভিযান করিয়া এবং দুৰ্বত্ত কর্ণাটলক্ষ্মী-লুণ্ঠনকারী শত্রুকুলকে ধ্বংস করিয়া শেষ বয়সে গঙ্গাতটে পুণ্যাশ্রমে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্বতঃই অনুমিত হয় যে সামন্তসেনই প্রথমে কর্ণাট হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া গঙ্গাতীরে বাস করেন। কিন্তু বল্লালসেনের নৈহাটি তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে চন্দ্রের বংশে জাত অনেক রাজপুত্র রাঢ়দেশের অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন এবং তাঁহাদের বংশে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন। এখানে স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, সামন্তসেনের পূর্ব্বপুরুষগণ রাঢ়দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এই দুইটি উক্তির সামঞ্জস্য সাধন করিতে হইলে বলিতে হয় যে কর্ণাটের এক সেনবংশ বহুদিন যাবৎ রাঢ়দেশে বাস করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহারা কর্ণাট দেশের সহিতও সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। এই বংশের সামন্তসেন যৌবনে কর্ণাট দেশে বহু যুদ্ধে নিজের শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়া এই বংশের উন্নতির সূত্রপাত করেন এবং সম্ভবত ইহার ফলেই তাঁহার পুত্র হেমন্তসেন রাঢ়দেশে একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।
কী উপায়ে বিদেশীয় সেনগণ সুদূর কর্ণাট দেশ হইতে আসিয়া বাংলায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাবধি সঠিক নির্ণীত হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে তাঁহারা প্রথমে পালরাজগণের অধীনে সৈন্যাধ্যক্ষ অথবা অন্য কোনো উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন। পরে পালরাজগণের দুর্বলতার সুযোগে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই অনুমানের সপক্ষে বলা যাইতে পারে যে পালরাজগণের তাম্রশাসনগুলিতে যে কর্ম্মচারীর তালিকা আছে তাঁহার মধ্যে নিয়মিতভাব ‘গৌড়-মালব-খশ-হূণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট-চাট-ভাট’ এই পদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সম্ভবত পালরাজগণ খশ হূণ প্রভৃতির ন্যায় কর্ণাটগণকেও সৈন্যদলে নিযুক্ত করিতেন এবং সেনবংশীয় তাহাদের নায়ক কোনো সুযোগে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র এক রাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন।
কেহ কেহ বলেন যে, কর্ণাটদেশীয় সেনরাজগণের পূর্ব্বপুরুষ কোনো আক্রমণকারী রাজার সহিত দাক্ষিণাত্য হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া প্রথমে শাসনকর্ত্তা বা সামন্তরাজরূপে প্রতিষ্ঠিত হন এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে সিন্ধিয়া হোলকার প্রভৃতি মহারাষ্ট্র নায়কগণের ন্যায় ক্রমে পশ্চিমবঙ্গে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কর্ণাটের চালুক্যরাজগণ যে একাধিকবার বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন তাহা পূর্ব্বেই। বলা হইয়াছে। যুবরাজ বিক্রমাদিত্য আ ১০৬৮ অব্দে গৌড় ও কামরূপ আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে ও পরে এইরূপ আরও বিজয়াভিযানের কথা চালুক্যগণের শিলালিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে। একখানি লিপি হইতে জানা যায় যে একাদশ শতাব্দীর শেষ অথবা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আচ নামক • চালুক্যরাজ বিক্রমাদিত্যের একজন সামন্ত বঙ্গ ও কলিঙ্গ রাজ্যে স্বীয় প্রভুর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ১১২১ ও ১১২৪ অব্দে উৎকীর্ণ লিপিতে বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গৌড়, মগধ ও নেপাল জয়ের উল্লেখ আছে। সুতরাং ইহা অসম্ভব নহে যে, এই সমস্ত অভিযানের ফলেই কর্ণাটবংশীয় সেনগণ বঙ্গদেশে এবং নান্যদেব মিথিলায় প্রভুত্ব স্থাপনের সুযোগ পাইয়াছিলেন।
কেহ কেহ অনুমান করেন যে সেনরাজগণের পূৰ্বপুরুষ চোলরাজ রাজেন্দ্ৰচোলের সঙ্গে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। কিন্তু রাজেন্দ্ৰচোল কর্ণাটবাসী ছিলেন না, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অনুমানই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয়।
সেনরাজগণ যে সময় এবং যেভাবেই বঙ্গদেশে আসিয়া থাকুন, সামন্তসেনের পূৰ্ব্বে তাঁহাদের কোনো বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় নাই। সামন্তসেন কর্ণাট দেশে অনেক যুদ্ধে যশোলাভ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে রাঢ়দেশে গঙ্গাতীরে বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কোনো স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ তাঁহার পৌত্র বিজয়সেনের শিলালিপিতে তাঁহার নামের সঙ্গে কোনো রাজত্বসূচক পদবী ব্যবহৃত হয় নাই। অপর পক্ষে বিজয়সেনের লিপিতে তাঁহার পিতা হেমন্তসেন মহারাজাধিরাজ ও মাতা যশোদেবী মহারাজ্ঞী উপাধীতে ভূষিত হইয়াছেন। সুতরাং হেমন্তসেনই এই বংশের প্রথম রাজা ছিলেন এই অনুমানই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু হেমন্তসেন সম্বন্ধে আর কোনো বিবরণ এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। যদিও পরবর্ত্তীকালে তাঁহার পুত্রের লিপিতে তাহাকে মহারাজাধিরাজ বলা হইয়াছে, তথাপি খুব সম্ভবত তিনি রামপালের অধীনস্থ একজন সামন্ত রাজা ছিলেন।
.
২. বিজয়সেন
হেমন্তসেনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিজয়সেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিজয়সেনের একখানি তাম্রশাসন ও একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাম্রশাসনখানিতে তাঁহার যে রাজ্যাঙ্ক লিখিত আছে তাঁহার প্রকৃত পাঠ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ ইহাকে ৩২ এবং কেহ কেহ ৬২ পাঠ করিয়াছেন। এই শেষোক্ত মতই এখন সাধারণত গৃহীত হইয়া থাকে এবং ইহা সত্য হইলে বিজয়সেন আ ১০৯৫ অব্দে রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। অপর পক্ষে তাম্ৰশাসনোক্ত রাজ্যাঙ্ক ৩২ পাঠ করিলে তিনি আ ১১২৫ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এরূপ অনুমানই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়।
পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে পালরাজ রামপাল আ ১০৭০ হইতে ১১২০ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সুতরাং যদি বিজয়সেন ১০৯৫ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার রাজত্বের প্রথম ১৫ বৎসর তিনি ক্ষুদ্র ভূখণ্ডের অধিপতি এবং অন্তত কিছুকাল রামপালের সামন্ত ছিলেন এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া মনে হয়। যে সমুদয় সামন্তরাজ রামপালকে বরেন্দ্র উদ্ধারে সাহায্য করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নিদ্রাবলীর বিজয়রাজ একজন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই বিজয়রাজই সেনরাজ বিজয়সেন। আবার বিজয়সেনের শিলালিপির ঊনবিংশ শ্লোকে গূঢ় শ্লেষ অর্থ কল্পনা করিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে বিজয়সেন কৈবর্ত্যরাজ দিব্যকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু এই অনুমান ভিত্তিহীন বলিয়াই মনে হয়।
রামপালের মৃত্যুর পর যখন পালরাজ্যে গোলযোগ উপস্থিত হইল তখনই বিজয়সেন স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করিবার সুযোগ পাইলেন। শূরবংশীয় রাজকন্যা বিলাসদেবী তাঁহার প্রধানা মহিষী ছিলেন। রামপালের সামন্ত রাজগণের মধ্যে অরণ্য প্রদেশস্থ সামন্তবর্গের চূড়ামণি অপরমারের অধিপতি লক্ষ্মীশূরের উল্লেখ আছে। রাজেন্দ্ৰচোলের লিপিতে দক্ষিণ রাঢ়ের অধিপতি রণশূরের নাম পাওয়া যায়। সুতরাং একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ রাঢ় অথবা ইহার অধিকাংশ শূরবংশীয় রাজগণের অধীনে ছিল। সম্ভবত বিলাসদেবী এই বংশীয় ছিলেন এবং তাঁহাকে বিবাহ করিয়া বিজয়সেন রাঢ়দেশে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন। কিন্তু কর্ণাটরাজের সামন্ত আচ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে প্রভুত্ব স্থাপনই সম্ভবত কর্ণাটদেশীয় বিজয়সেনের শক্তিবৃদ্ধির প্রধান কারণ।
যে উপায়ে হউক বিজয়সেন যে রামপালের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই সমগ্র বঙ্গদেশে প্রভুত্ব স্থাপনের প্রয়াসী হইয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি বৰ্ম্মরাজকে পরাজিত করিয়া পূৰ্ব্ব ও দক্ষিণবঙ্গ অধিকার করেন। তাঁহার দেওপাড়া শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে যে নান্য, বীর, রাঘব ও বর্দ্ধন নামক রাজগণ তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাভূত হন এবং তিনি কামরূপরাজকে দূরীভূত, কলিঙ্গরাজকে পরাজিত এবং গৌড়রাজকে দ্রুত পলায়ন করিতে বাধ্য করেন।
বিজয়সেনের ন্যায় কর্ণাটদেশীয় নান্যদেব মিথিলায় রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্ভবত তিনিও বঙ্গদেশ অধিকার করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং এই সূত্রেই বিজয়সেনের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নান্যদেব বঙ্গজয়ের আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বীর, বর্দ্ধন ও রাঘব এই তিনজন রাজা কোথায় রাজত্ব করিতেন তাহা নিশ্চিত বলা যায় না।
বিজয়সেন কর্ত্তৃক পরাজিত গৌড়রাজ যে মদনপাল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। রাজসাহী জিলার অন্তর্গত দেওপাড়া নামক স্থানে বিজয়সেনের যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে তিনি ঐ স্থানে প্রদ্যুম্নেশ্বরের এক প্রকাণ্ড মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। সুতরাং বরেন্দ্রের অন্তত এক অংশ যে বিজয়সেনের রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কামরূপ ও কলিঙ্গের অভিযানের ফলে বিজয়সেন কী পরিমাণ ঐ দুই রাজ্যে স্বীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন তাহা নিশ্চিত বলা যায় না, কিন্তু ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে সমগ্র পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গে বিজয়সেনের আধিপত্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কারণ তাহা না হইলে তাঁহার পক্ষে কামরূপ ও কলিঙ্গে কোনো অভিযান প্রেরণ করা সম্ভবপর ছিল বলিয়া মনে হয় না।
এইরূপে বহু যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিজয়সেন প্রায় সমগ্র বাংলা দেশে এক অখণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পালরাজগণ মগধে আশ্রয় লইয়াছিলেন। বরেন্দ্রের এক অংশে তাঁহাদের কোনো আধিপত্য ছিল কি না বলা যায় না, কিন্তু বঙ্গদেশের অন্য কোনো স্থানে তাঁহাদের যে কোনো প্রকার প্রভুত্বই। ছিল না সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই।
দেওপাড়া লিপিতে উল্লিখিত হইয়াছে যে পাশ্চাত্য চক্র জয় করিবার জন্য বিজয়সেনের নৌ-বিতান গঙ্গা নদীর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হইয়াছিল। এই রণসজ্জার উদ্দেশ্য ও ফলাফল কিছুই নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। সম্ভবত মগধের পাল ও গাহড়বাল এই দুই রাজশক্তির বিরুদ্ধেই ইহা প্রেরিত হইয়াছিল। যদি ইহা রাজমহল অতিক্রম করিয়া থাকে তাহা হইলে বলিতে হইবে যে বরেন্দ্র ও মিথিলা এই উভয় প্রদেশেই বিজয়সেনের শক্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা যে বিশেষ সফল হইয়াছিল দেওপাড়া লিপির বর্ণনা হইতে এরূপ মনে হয় না।
বিজয়সেনের রাজত্ব বাংলার ইতিহাসে বিশেষ একটি স্মরণীয় ঘটনা। বহুদিন পরে আবার একটি দৃঢ় রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশে সুখ ও শান্তি আনয়ন করিয়াছিল। পালরাজত্বের শেষ যুগে বাংলার রাজনৈতিক একতা বিনষ্ট হইয়াছিল এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজগণ স্বীয় স্বার্থের প্রেরণায় বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের আদর্শ ভুলিয়া পরস্পর কলহে মত্ত ছিলেন। অর্থ ও রাজ্যের লোভ দেখাইয়া রামপাল ইহাদিগকে কিছুদিনের জন্য স্বপক্ষে আনিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাদিগকে দমন করিয়া দৃঢ় অখণ্ড রাজশক্তির প্রভাব পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। বিজয়সেন ইহা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের প্রবল প্রতাপে বাংলায় এক নূতন গৌরবময় যুগের সূচনা হইল। বিজয়সেন এইরূপ কঠোর শাসনের প্রবর্ত্তন না করিলে বাংলা দেশে পুনরায় অরাজকতা ও মাৎস্যন্যায়ের প্রাদুর্ভাব হইত। সাধারণত একজন সামন্তরাজের পদ হইতে নিজের বুদ্ধি সাহস ও রণ-কৌশলে বিজয়সেন বাংলার সার্বভৌম রাজার স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব ও অসামান্য ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। তিনি পরমেশ্বর পরমভট্টারক ও মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অরিরাজ-বৃষভশঙ্কর এই গৌরবসূচক নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁহার রাজত্বে যে বাংলায় নবযুগের সূত্রপাত হইয়াছিল কবি উমাপতিধর রচিত দেওপাড়া প্রশস্তি তাঁহার সাক্ষ্য দিতেছে। অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইলেও এই প্রশস্তির মধ্যে এক নবজাগ্রত জাতি ও রাজশক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ প্রতিধ্বনিত হইয়াছে এবং বিজয়সেনের এক বিরাট মহিমাময় চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ কবি শ্রীহর্ষ-রচিত বিজয়-প্রশস্তি ও গৌড়োৰ্ব্বীশ-কুল-প্রশস্তি বিজয়সেনের উদ্দেশ্যেই লিখিত হইয়াছিল এরূপ মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে।
.
৩. বল্লালসেন
আ ১১৫৮ অব্দে বিজয়সেনের মৃত্যু হয় এবং তৎপুত্র বল্লালসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। বল্লালসেনের একখানি তাম্রশাসন এবং তাঁহার রচিত দানসাগর এবং অদ্ভুতসাগর নামক দুইখানি গ্রন্থ হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু কিছু বিবরণ জানা যায়। এতদ্ব্যতীত ‘বল্লাল-চরিত’ নামক দুইখানি গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাতে বল্লালসেনের অনেক কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। বল্লালচরিতের একখানি গ্রন্থের পুস্পিকা হইতে জানা যায় যে ইহার প্রথম দুই খণ্ড বল্লালসেনের অনুরোধে তাঁহার শিক্ষক গোপালভট্ট কর্ত্তৃক ১৩০০ শকাব্দে, এবং তৃতীয় খণ্ড নবদ্বীপাধিপতির আদেশে গোপালভট্টের বংশধর আনন্দভট্ট কর্ত্তৃক ১৫০০ শকাব্দে রচিত হইয়াছিল। বল্লালচরিতের দ্বিতীয় গ্রন্থ নবদ্বীপের রাজা বুদ্ধিমন্তখানের আদেশে আনন্দভট্ট কর্ত্তৃক ১৪৩২ শকাব্দে রচিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে প্রথম গ্রন্থখানি জাল এবং দ্বিতীয় গ্রন্থখানিই প্রকৃত বল্লালচরিত। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন। উভয় গ্রন্থই কতকগুলি বংশাবলী এবং জনপ্রবাদের সমষ্টিমাত্র এবং ইহার কোনোখানিই প্রামাণিক বা অকৃত্রিম বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সম্ভবত ষোড়শ কি সপ্তদশ শতাব্দীতে কেবলমাত্র প্রচলিত কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়াই এই গ্রন্থ দুইখানি লিখিত হইয়াছিল এবং উনবিংশ শতাব্দীতেও ইহার কোনো কোনো অংশ পরিবর্তিত অথবা পরিবর্ধিত হইয়াছে। সুতরাং বল্লালচরিতের কোনো উক্তি অন্য প্রমাণাভাবে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত নহে।
দানসাগর ও অদ্ভুতসাগরের উপসংহারে বল্লালসেনের পরিচায়ক কয়েকটি শ্লোক আছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, গুরু অনিরুদ্ধের নিকট বল্লালসেন বেদস্মৃতিপুরাণ প্রভৃতি বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। বল্লালসেন যে যাগযজ্ঞাদি ধৰ্ম্মানুষ্ঠানে রত প্রবীণ শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ছিলেন তাঁহার রচিত উক্ত দুইখানি গ্রন্থই তাঁহার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। এদেশে বল্লালসেনের সম্বন্ধে যে সমুদয় প্রবাদ প্রচলিত আছে তাহাও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করে। বঙ্গীয় কুলজী গ্রন্থে কৌলিন্য প্রথার উৎপত্তির সহিত বল্লালসেনের নাম অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বাংলা দেশ বিজয়সেনকে ভুলিয়া গিয়াছে কিন্তু বল্লালসেনের নাম ও স্মৃতি এদেশ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। খুব সম্ভবত বল্লালসেনের একটি বিরাট গ্রন্থালয় ছিল দুই-তিন শত বৎসর পরেও ইহা বর্ত্তমান ছিল, অন্তত ইহার সম্বন্ধে জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল। রঘুনন্দন প্রণীত স্মৃতিতত্ত্বের একখানি পুঁথিতে বল্লালসেন দেবাহৃত দ্বিখণ্ডাক্ষর লিখিত ‘শ্রীহয়শীর্ষপঞ্চরাত্রেয়’ পুস্তকের উল্লেখ আছে।
প্রধানত যাগযজ্ঞ, শাস্ত্রচর্চ্চা ও সমাজসংস্কার প্রভৃতি কার্যে নিযুক্ত থাকিলেও বল্লালসেন যুদ্ধবিগ্রহ হইতে একেবারে নিরস্ত্র থাকিতে পারেন নাই। অদ্ভুতসাগরে তাঁহাকে “গৌড়েন্দ্র-কুঞ্জরালান-স্তম্ভবাহুর্মহীপতিঃ” বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে গৌড়রাজের সহিত তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই গৌড়রাজ সম্ভবত গোবিন্দপাল, কারণ তিনি গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করিতেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে গোবিন্দপাল মগধে রাজত্ব করিতেন এবং ১১৬২ অব্দে তাঁহার রাজ্য বিনষ্ট হয়। সুতরাং খুব সম্ভব বল্লালসেনের হস্তেই তিনি পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত হন। বল্লালচরিতে বল্লালসেনের মগধ-জয়ের উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে আরও উক্ত হইয়াছে যে পিতার জীবদ্দশায় তিনি মিথিলা জয় করেন। মিথিলা যে সেনরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এরূপ অনুমান করিবার সঙ্গত কারণ আছে। প্রথমত নান্যদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগে মিথিলার কোনো বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ ঐ দেশীয় ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয় নাই। দ্বিতীয়ত প্রচলিত ও সুপ্রসিদ্ধ জনপ্রবাদ অনুসারে বল্লালসেন স্বীয় রাজ্য রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগড়ী, বঙ্গ ও মিথিলা এই পাঁচভাগে বিভক্ত করেন। তৃতীয় বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেনের নামযুক্ত সংবৎ মিথিলায় অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। মিথিলার বাহিরে অন্য কোনো স্থানে এই অব্দ জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মিথিলা সেনরাজ্যভুক্ত না হইলে তথায় এই অব্দ প্রচলনের কোনো ন্যায়সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। সুতরাং বল্লালসেন মিথিলা জয় করিয়াছিলেন এই প্রবাদ সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।
বল্লালসেন যে পিতৃরাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে। সম্ভবত মিথিলা ও মগধের কতকাংশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। তিনি চালুক্যরাজের (সম্ভবত দ্বিতীয় জগদেবমল্ল) দুহিতা রামদেবীকে বিবাহ করেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে সেনরাজগণের সম্মান ও প্রতিপত্তি বাংলার বাহিরে বিস্তৃত হইয়াছিল এবং পিতৃভূমি কর্ণাটের সহিতও তাঁহাদের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় নাই। পিতার অনুকরণে বল্লালসেন সম্রাটসূচক অন্যান্য পদবীর সহিত ‘অরিরাজ নিঃশঙ্কশঙ্কর’ এই নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বল্লালসেন যে কেবল রাজগণের নহে বিদ্বানমণ্ডলীরও চক্রবর্ত্তী ছিলেন প্রশস্তিকারের এই উক্তি অনেকাংশে সত্য।
শস্ত্রচালনা ও শাস্ত্রচর্চ্চায় জীবন অতিবাহিত করিয়া রাজর্ষিতুল্য বল্লালসেন বৃদ্ধ বয়সে পুত্র লক্ষ্মণসেনের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ এবং তাঁহাকে সাম্রাজ্যরক্ষারূপ মহাদীক্ষায় দীক্ষিত করিয়া সস্ত্রীক ত্রিবেণীর নিকট গঙ্গাতীরে বানপ্রস্থ অবলম্বনপূৰ্ব্বক শেষ জীবন অতিবাহিত করেন। অদ্ভুতসাগরের একটি শ্লোক হইতে আমরা এই বিবরণ পাই। এই শ্লোকের এরূপ অর্থও করা যাইতে পারে যে বৃদ্ধ রাজা ও রাণী স্বেচ্ছায় গঙ্গাগর্ভে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।
.
৪. লক্ষ্মণসেন
১১৭৯ অব্দে লক্ষ্মণসেন পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজ্যকালের আটখানি তাম্রশাসন, তাঁহার সভাকবিগণ রচিত কয়েকটি স্তুতিবাচক শ্লোক, তাঁহার পুত্রদ্বয়ের তাম্রশাসন ও মুসলমান ঐতিহাসিক মীনহাজুদ্দিন বিরচিত তবকাং-ই নাসিরী নামক গ্রন্থ হইতে তাঁহার রাজ্যের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। বাল্যকালেই তিনি পিতা ও পিতামহের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া রণকুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তাঁহার দুইখানি তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে তিনি কৌমারে উদ্ধত গৌড়েশ্বরের শ্রীহরণ ও যৌবনে কলিঙ্গ দেশে অভিযান করিয়াছিলেন; তিনি যুদ্ধে কাশিরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং ভীরু প্ৰাগজ্যোতিষের (কামরূপ আসাম) রাজা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে বিজয়সেন ও বল্লালসেন উভয়েই গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সুতরাং খুব সম্ভবত কুমার লক্ষ্মণসেন পিতা অথবা পিতামহের রাজত্বকালে গৌড়ে যে অভিযান করিয়াছিলেন প্রশস্তিকার এস্থলে তাঁহারই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রশস্তিকার অন্যত্র লিখিয়াছেন যে লক্ষ্মণসেন নিজভুজবলে সমর-সমুদ্র মন্থন করিয়া গৌড়লক্ষ্মী লাভ করিয়াছিলেন। বিজয়সেন গৌড়রাজাকে দূরীভূত করিলেও তাঁহার রাজ্যকালে গৌড়বিজয় সম্ভবত সম্পূর্ণ হয় নাই। কারণ গোবিন্দপাল গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করিতেন এবং বল্লালসেনকে গৌড়ে অভিযান করিতে হইয়াছিল। লক্ষ্মণসেনই সম্ভবত সম্পূর্ণরূপে গৌড়দেশ জয় করেন। কারণ রাজধানী গৌড়ের লক্ষ্মণাবতী এই নাম সম্ভবত লক্ষ্মণসেনের নাম অনুসারেই হইয়াছিল এবং সৰ্ব্বপ্রথম তাঁহার তাম্রশাসনেই সেনরাজগণের নামের পূর্ব্বে গৌড়েশ্বর এই উপাধি ব্যবহৃত হইয়াছিল।
লক্ষ্মণসেনের কলিঙ্গ ও কামরূপ জয়ও সম্ভবত তাঁহার পিতামহের রাজ্যকালেই সংঘটিত হইয়াছিল। কারণ বিজয়সেনের রাজ্যকালেই এই দুই দেশ বিজিত হইয়াছিল। তবে ইহাও অসম্ভব নহে যে গৌড়ের ন্যায় এই দুই রাজ্যও লক্ষ্মণসেনই সম্পূর্ণরূপে জয় করেন এবং এইজন্য তাঁহাকে পুনরায় যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। কারণ তাঁহার পুত্রদ্বয়ের তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে তিনি সমুদ্রতীরে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে, কাশীতে ও প্রয়াগে যজ্ঞকূপের সহিত ‘সমরজয়স্তম্ভ’ স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে গঙ্গাবংশীয় রাজগণ কলিঙ্গ ও উৎকল উভয় দেশেই রাজত্ব করিতেন। সম্ভবত লক্ষ্মণসেন কোনো গঙ্গরাজাকে পরাজিত করিয়াই পুরীতে জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন।
কাশী ও প্রয়াগে জয়স্তম্ভ স্থাপন পশ্চিম দিকে গাহড়বাল রাজার বিরুদ্ধে তাঁহার বিজয়াভিযান সূচিত করিতেছে। পালবংশের পতনের পূর্ব্বেই যে গাহড়বাল রাজগণ মগধে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিজয়সেন নৌবাহিনী পাঠাইয়াও তাহাদের বিরুদ্ধে বিশেষ কোনো জয়লাভ করিতে পারেন নাই। বল্লালসেন কিছু সফলতা লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু গোবিন্দপালের রাজ্য নষ্ট করায় গাহড়বালগণ মগধে আরও অধিকার বিস্তারের সুযোগ পাইলেন। গাহড়বালরাজ বিজয়চন্দ্র ও জয়চন্দ্রের লিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে, ১১৬৯ হইতে ১১৯০ অব্দের মধ্যে মগধের পশ্চিম ও মধ্যভাগ গাহড়বাল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। গাহড়বাল রাজ্যের পূর্ব্বদিকে এইরূপ দ্রুত বিস্তার সেনরাজ্যের পক্ষে বিশেষ আশঙ্কাজনক হওয়ায় লক্ষ্মণসেনের সহিত গাহড়বাল রাজ্যের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছিল। বিস্তৃত বিবরণ জানা না থাকিলেও লক্ষ্মণসেন যে এই যুদ্ধে বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। মগধের মধ্যভাগে গয়া জিলায় যে লক্ষ্মণসেন রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন বৌদ্ধগয়ায় প্রাপ্ত দুইখানি লিপিতে তাঁহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। গাহড়বালরাজ জয়চন্দ্রের লিপি হইতে প্রমাণিত হয় যে, ১১৮২ হইতে ১১৯২ অব্দের মধ্যে তিনি গয়ায় রাজত্ব করিতেন। তাঁহাকে পরাজিত না করিয়া লক্ষ্মণসেন কখনো গয়া অধিকার করিতে পারেন নাই। লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক জয়চন্দ্রের পরাজয়ের এরূপ স্পষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান থাকায় লক্ষ্মণসেন যে কাশী ও প্রয়াগে জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন তাম্রশাসনের এই বিশিষ্ট উক্তি নিছক কল্পনা মনে করিয়া অগ্রাহ্য করিবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।
এইরূপে দেখা যায় যে, উত্তরে গৌড়, পূৰ্ব্বে কামরূপ ও দক্ষিণে কলিঙ্গরাজকে পরাভূত করিয়া লক্ষ্মণসেন পৈত্রিক রাজ্য অক্ষুণ্ণ এবং সুদৃঢ় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পশ্চিমে তিনি স্বীয় পিতা ও পিতামহ অপেক্ষা অধিকতর সফলতা অর্জন করিয়াছিলেন এবং অন্তত মগধে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু ও সেনরাজ্য ধ্বংসের বহুকাল পরেও মগধে তাঁহার রাজ্য শেষ হইতে সংবৎসর গণনা করা হইত। মগধে লক্ষ্মণসেনের ক্ষমতা যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ইহাই তাঁহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।
লক্ষ্মণসেনের দুই সভাকবি উমাপতিধর ও শরণ রচিত কয়েকটি শ্লোকে এক রাজার বিজয়কাহিনীর উল্লেখ আছে। শ্লোকগুলিতে রাজার নাম নাই কিন্তু তিনি যে প্ৰাগজ্যোতিষ (কামরূপ), গৌড়, কলিঙ্গ, কাশী, মগধ প্রভৃতি জয় করিয়াছিলেন এবং চেদি ম্লেচ্ছরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন তাঁহার উল্লেখ আছে। এই সমুদয় শ্লোক যে লক্ষ্মণসেনকে উদ্দেশ্য করিয়াই তাঁহার সভাকবিরা রচনা করিয়াছিলেন এরূপ সিদ্ধান্ত অনায়াসেই করা যাইতে পারে। কারণ চেদি ও ম্লেচ্ছরাজের পরাজয় ব্যতীত অন্যান্য বিজয়কাহিনী যে লক্ষ্মণসেনের সম্বন্ধে প্রযোজ্য পূর্ব্বেই তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং লক্ষ্মণসেন যে চেদি (কলচুরি) ও কোনো ম্লেচ্ছরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। রতনপুরের কলচুরিরাজগণের সামন্ত বল্লভরাজ গৌড়রাজকে পরাভূত করিয়াছিলেন, মধ্যপ্রদেশের একখানি শিলালিপিতে এরূপ উল্লেখ আছে। সুতরাং লক্ষ্মণসেনের সহিত চেদিরাজের সংঘর্ষ সম্ভবত ঐতিহাসিক ঘটনা। এই যুদ্ধে দুই পক্ষই জয়ের দাবি করিয়াছেন-সুতরাং ইহার ফলাফল অনিশ্চিত বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।
উল্লিখিত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, লক্ষ্মণসেন বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় সারা জীবনই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত ছিলেন। ধর্ম্মপাল ও দেবপালের পরে বাংলার আর কোনো রাজা তাঁহার ন্যায় বাংলার সীমান্তের বাহিরে যুদ্ধে এরূপ সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু যুদ্ধ ব্যবসায়ী হইলেও রাজা লক্ষ্মণসেন শাস্ত্র ও ধর্ম্মচর্চ্চায় পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। বল্লালসেন তাঁহার অদ্ভুতসাগর গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। পিতার নির্দেশক্রমে লক্ষ্মণসেন এই গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। লক্ষ্মণসেন নিজে সুকবি ছিলেন এবং তাঁহার রচিত কয়েকটি শ্লোক পাওয়া গিয়াছে। ঘোয়ী, শরণ, জয়দেব, গোবর্দ্ধন এবং উমাপতিধর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণ তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন। তাঁহার প্রধানমন্ত্রী ও ধর্ম্মাধ্যক্ষ হলায়ূধ ভারত প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। জয়দেব এখনো একজন শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবি বলিয়া জগদ্বিখ্যাত। তাঁহার মধুর বৈষ্ণব পদাবলী এখনো ভারতের ঘরে ঘরে গীত হইয়া থাকে।
লক্ষ্মণসেন নিজেও বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুরাগী ছিলেন। বিজয় সেন ও বল্লালসেন পরম-মাহেশ্বর উপাধি ধারণ করিতেন। তাঁহাদের তাম্রশাসনে প্রথমেই শিবের প্রণাম ও স্তুতিবাচক শ্লোক এবং মুদ্রায় কুলদেবতা সদাশিবের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিত। লক্ষ্মণসেন সদাশিব মুদ্রার পরিবর্ত্তন করেন নাই কিন্তু তিনি পরম-মাহেশ্বরের পরিবর্তে পরমবৈষ্ণব উপাধি গ্রহণ করেন এবং তাঁহার তাম্রশাসনগুলি নারায়ণের প্রণাম ও স্তুতিবাচক শ্লোক দিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। সুতরাং লক্ষ্মণসেন কৌলিক শৈবধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন ইহাই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়।
লক্ষ্মণসেন যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁহার বয়স প্রায় ষাট বৎসর। প্রায় ২০ বৎসর রাজত্ব করিয়া এই অশীতিপর বৃদ্ধ রাজা পিতার ন্যায় গঙ্গাতীরে অবস্থান করিবার উদ্দেশ্যে নবদ্বীপে গমন করেন। তাঁহার এই শেষ বয়সে রাজ্যে আভ্যন্তরিক বিপ্লবের সূচনা দেখা যায়। ১১৯৬ অব্দের একখানি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, ডোম্মনপাল নামক এক ব্যক্তি সুন্দরবনের খাড়ী পরগণায় বিদ্রোহী হইয়া এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। এই সময় আর্য্যাবর্তেও বিষম বিপদ উপস্থিত হয়। তুরস্কজাতীয় ঘোর দেশের অধিপতি মহম্মদ ঘোরী চৌহান পৃথ্বীরাজ ও গাহড়বাল জয়চন্দ্রকে পরাজিত করিয়া ক্রমে ক্রমে প্রায় সমগ্র হিন্দুস্থানে নিজের রাজ্য বিস্তার করেন। আর্য্যাবর্তের প্রসিদ্ধ রাজপুত রাজ্যগুলি একে একে বিজেতা তুর্কীগণের পদানত হয়। ক্রমে তুর্কীগণ যুক্তপ্রদেশ অধিকার করিয়া মগধের সীমান্তে উপনীত হইল।
এই ঘোর দুর্দিনে লক্ষ্মণসেন স্বীয় রাজ্য রক্ষার কী উদ্যোগ করিয়াছিলেন তাহা জানিবার কোনো উপায় নাই। বাঙ্গালী অথবা ভারতীয় কোনো লেখক রচিত দেশের এই দুর্যোগময় যুগের কোনো বিবরণই পাওয়া যায় নাই। ইহার অর্দ্ধশতাব্দী পরে তুর্কী বিজেতার সভাসদ ঐতিহাসিক লোকমুখে সেনরাজ্য জয়ের যে কাহিনী শুনিয়াছিলেন তাহা অবলম্বন করিয়াই এই যুগের ইতিহাস রচিত হইয়াছে। আর সেই ইতিহাসেরও প্রকৃত মর্ম গ্রহণ না করিয়া তাঁহার বিকৃত ব্যাখ্যান দ্বারা কেহ কেহ প্রচার করিয়াছেন যে ১৭ জন তুরস্ক অশ্বারোহী বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিল এবং এই অদ্ভুত উপাখ্যানে বিশ্বাস করিয়া অনেকেই লক্ষ্মণসেনকে কাপুরুষ বলিয়া হতশ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছে। এইজন্যই এই বিষয়টির একটু বিস্তৃত আলোচনা প্রয়োজন।
.
৫. তুরস্ক সেনা কর্ত্তৃক গৌড় জয়
তবকাৎ-ই-নাসিরী নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থে তুরস্কগণ কর্ত্তৃক মগধ ও গৌড় জয়ের সৰ্ব্বপ্রাচীন বিবরণ পাওয়া যায়। গ্রন্থকার মীনহাজুদ্দিন দিল্লীর সুলতানের অধীনে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং নানা স্থানে ঘুরিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আ ১২৬০ অব্দের কিছু পরে এই ইতিহাস রচনা করেন। গৌড় ও মগধ জয়ের সম্বন্ধে কোনো সরকারী বিবরণ বা দলিল তাঁহার হস্তগত হয় নাই। মগধ জয়ের ৪০ বৎসর পরে লক্ষ্মণাবতী নগরীতে দুইজন বৃদ্ধ সৈনিকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইহারা এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল এবং ইহাদের নিকট শুনিয়াই মীনহাজ মগধ জয়ের বিবরণ লিখিয়াছেন। গৌড়ের অভিযানে লিপ্ত ছিল এরূপ কোনো ব্যক্তির সহিত সম্ভবত তাঁহার দেখা হয় নাই। কারণ তিনি কেবলমাত্র বলিয়াছেন যে বিশ্বাসী লোকদের নিকট হইতে তিনি গৌড় বিজয়ের কাহিনী শুনিয়াছেন।
এইরূপে অর্দ্ধশতাব্দী পরে কেবলমাত্র লোকমুখে শুনিয়া মীনহাজ মগধ ও গৌড় জয়ের যে ঐতিহাসিক বিবরণ লিখিয়াছেন তাঁহার সারমর্ম নিম্নে দেওয়া হইল :
“মুহম্মদ বখতিয়ার নামক খিলজীবংশীয় একজন তুরস্ক সেনানায়ক উপযুক্ত কৰ্ম্মানুসন্ধানে মহম্মদ ঘোরী ও কুতবুদ্দিনের নিকট গিয়া বিফলমনোরথ হইয়া অবশেষে অযোধ্যায় মালিক হুসামুদ্দিনের অনুগ্রহে চুনারগড়ের নিকট দুইটি পরগণা জায়গীরপ্রাপ্ত হন। এখান হইতে বখতিয়ার দুই বত্সর যাবৎ মগধের নানা স্থান লুণ্ঠন করেন এবং লুণ্ঠিত অর্থের দ্বারা সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া অবশেষে দুইশত অশ্বারোহী সৈন্যসহ হঠাৎ আক্রমণ করিয়া ‘কিল্লা বিহার’ অধিকার করেন। ইহার মুণ্ডিত-মস্তক অধিবাসীদিগকে নিহত ও বিস্তর দ্রব্য লুণ্ঠন করার পরে আক্রমণকারীগণ জানিতে পারিলেন যে, ইহা বস্তুত ‘কিল্লা’ বা দুর্গ নহে, একটি বিদ্যালয় মাত্র, এবং হিন্দুর ভাষায় ইহাকে ‘বিহার’ বলে।
“কিল্লা বিহারের লুণ্ঠিত ধনরত্নসহ বখতিয়ার স্বয়ং দিল্লীতে গিয়া কুতবুদ্দিনের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বহু সম্মান প্রাপ্ত হন। দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি বিহার প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন।
“এই সময়ে রায় লখমনিয়া রাজধানী ‘নদিয়া’তে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুসময়ে তিনি মাতৃগর্ভে ছিলেন। তাঁহার জন্মকালে দৈবজ্ঞগণ গণনা করিয়া বলিল যে যদি এই শিশুর এখনই জন্ম হয় তবে সে কখনোই রাজা হইবে না, কিন্তু আর দুই ঘণ্টা পরে জন্মিলে সে ৮০ বৎসর রাজত্ব করিবে। এই কথা শুনিয়া রাজমাতার আদেশে তাঁহার দুই পা বাঁধিয়া মাথা নিচের দিকে করিয়া তাঁহাকে ঝুলাইয়া রাখা হইল। শুভ মুহূর্ত উপস্থিত হইলে তাঁহাকে নামানো হয়, কিন্তু পুত্র প্রসবের পরেই তাঁহার মৃত্যু হইল। রায় লখমনিয়া ৮০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং হিন্দুস্থানের একজন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন।
“বখতিয়ার কর্ত্তৃক বিহার জয়ের পরে তাঁহার বীরত্বের খ্যাতি নদীয়ায় পৌঁছিল। দৈবজ্ঞ, পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণগণ রাজাকে বলিলেন, ‘শাস্ত্রে লেখা আছে তুরস্কেরা এ দেশ জয় করিবে, এবং তাঁহার কাল উপস্থিত, সুতরাং অবিলম্বে পলায়ন করাই সঙ্গত।’ রাজার প্রশ্নোত্তরে তাঁহারা জানাইলেন যে তুরস্ক বিজয়ীর চেহারা কিরূপ তাহাও শাস্ত্রে লেখা আছে। গুপ্তচর পাঠাইয়া বখতিয়ারের আকৃতির বিবরণ আনানো হইলে দেখা গেল যে শাস্ত্রের বর্ণনার সহিত ইহার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। তখন বহু ব্রাহ্মণ ও বণিকগণ নদীয়া হইতে পলায়ন করিল, কিন্তু রাজা লখমনিয়া রাজধানী ত্যাগ করিতে স্বীকৃত হইলেন না।
“ইহার এক বৎসর পরে বখতিয়ার একদল সৈন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া বিহার হইতে যাত্রা করিলেন। তিনি এরূপ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন যে যখন অতর্কিতভাবে তিনি সহসা নদীয়া পৌঁছিলেন, তখন মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী তাঁহার সঙ্গে আসিতে পারিয়াছিল, বাকী সৈন্য পশ্চাতে আসিতেছিল। নগরদ্বারে উপস্থিত হইয়া বখতিয়ার কাহাকেও কিছু না বলিয়া এমন ধীরেসুস্থে সঙ্গীগণসহ শহরে প্রবেশ করিলেন যে লোকেরা মনে করিল যে, সম্ভবত ইহারা একদল সওদাগর, অশ্ব বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। বখতিয়ার যখন রাজপ্রাসাদের দ্বারে উপনীত হইলেন তখন বৃদ্ধ রাজা লখমনিয়া মধ্যাহ্নভোজন করিতেছিলেন। সহসা প্রাসাদদ্বারে এবং নগরীর অভ্যন্তর হইতে তুমুল কলরব শোনা গেল। লখমনিয়া এই কলরবের প্রকৃত কারণ জানিবার পূর্ব্বেই বখতিয়ার সদলে রাজপুরীতে প্রবেশ করিয়া রাজার অনুচরগণকে হত্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। তখন রাজা নগ্নপদে প্রাসাদের পশ্চাৎ দ্বার দিয়া বাহির হইয়া নৌকাযোগে পলায়ন করিলেন। বখতিয়ারের সমুদয় সেনা নদীয়ায় উপস্থিত হইয়া ঐ নগরী ও তাঁহার চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ অধিকার করিল এবং বখতিয়ারও সেখানেই বসতি স্থাপন করিলেন। ওদিকে রায় লখমনিয়া সঙ্কনাৎ ও বঙ্গের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তথায় অল্পদিন পরেই তাঁহার রাজ্য শেষ হইল, কিন্তু তাঁহার বংশধরগণ এখনো বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেছেন।
“রায় লখমনিয়ার রাজ্য অধিকার করার পরে বখতিয়ার ধ্বংসপ্রায় নদীয়া ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমানে যে স্থান লক্ষ্মণাবতী নামে পরিচিত সেই স্থানে রাজধানী স্থাপন করিলেন।”
বখতিয়ার খিলজী কর্ত্তৃক বাংলা দেশ জয় সম্বন্ধে যত কাহিনী ও মতবাদ প্রচলিত আছে তাহা উল্লিখিত বিবরণের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ এ সম্বন্ধে অন্য কোনো সমসাময়িক ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায় নাই। মীনহাজুদ্দিনের বিবরণ সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করিলেও প্রচলিত বিশ্বাস অনেক পরিমাণে ভ্রান্ত বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবে। প্রথমত “সপ্তদশ অশ্বারোহী যবনের ডরে” কাপুরুষ লক্ষ্মণসেন “সোনার বাংলা রাজ্য” বিসর্জন দিয়াছিলেন, কবিবর নবীনচন্দ্রের এই উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। বখতিয়ার যখন নগরদ্বারে উপনীত হইয়াছিলেন তখন তাঁহার সহিত মাত্র ১৮ জন অশ্বারোহী সৈন্য ছিল, কিন্তু বাকী সৈন্য নিকটেই পশ্চাতে ছিল। কারণ যে সময় বখতিয়ার রাজবাড়ী পৌঁছিয়াছিলেন সেই সময়ই এই সৈন্য বা অন্তত তাঁহার এক বড় অংশ শহরে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার ফলে নগরমধ্যে যে আর্তনাদ উঠিয়াছিল বখতিয়ার রাজপ্রাসাদে প্রবেশের পূর্ব্বেই রাজার কর্ণে তাহা প্রবেশ করিয়াছিল। সুতরাং লক্ষ্মণসেন যখন পলায়ন করিয়াছিলেন তখন বখতিয়ারের বহু সৈন্য নগরমধ্যে ছিল। তারপর যখন সকল সৈন্য পৌঁছিল তখনই নদীয়া অধিকৃত হইল। বখতিয়ারের এই দিনকার অভিযানে কেবল এই নগরটিই অধিকৃত হইয়াছিল-সমস্ত বঙ্গদেশ তো দূরের কথা গৌড়ের অপর কোনো অংশই বিজিত হয় নাই।
যখন তুরস্ক আক্রমণের আশঙ্কায় নদীয়ার অধিবাসীরা বৎসরাবধি অন্যত্র পলাইতে ব্যস্ত ছিল তখন এই অশীতিপর বৃদ্ধ রাজা মন্ত্রী, দৈবজ্ঞ ও সভাসদ পণ্ডিতগণের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া রাজধানীতেই অবস্থান করিতেছিলেন। সুতরাং প্রজাবৰ্গ অপেক্ষা রাজার শৌর্য্য ও সাহস অনেক বেশী পরিমাণেই ছিল। যখন নগররক্ষীগণের মূর্খতায় বা অন্য কোনো কারণে বিনা বাধায় তুরস্ক সৈন্যগণ রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিল, তখন অতর্কিত সহসা আক্রান্ত হইয়া বৃদ্ধ রাজার পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করা ভিন্ন আর কোনো উপায় ছিল না। সুতরাং ইহাকে কোনোমতেই কাপুরুষতার দৃষ্টান্ত বলা যায় না।
মীনহাজুদ্দিনের বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া যাহারা লক্ষ্মণসেনের চরিত্রে দোষারোপ করেন তাঁহারা ভুলিয়া যান যে মীনহাজুদ্দিন স্বয়ং তাঁহার বহু সুখ্যাতি করিয়াছেন। তিনি লক্ষ্মণসেনকে হিন্দুস্থানের “রায়গণের পুরুষানুক্রমিক খলিফাস্থানীয়” বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং মীনহাজুদ্দিনের মতে লক্ষ্মণসেন আর্য্যাবর্তের রাজগণের মধ্যে সৰ্ব্বপ্রধান ছিলেন। তিনি পৃথ্বীরাজ ও জয়চাঁদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বলেন নাই, কিন্তু লক্ষ্মণসেনের জন্মকাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া তাঁহার দানশীলতার সুখ্যাতি ও শাসনরীতির প্রশংসা করিয়াছেন। এমনকি সাধারণত মুসলমান লেখকেরা অমুসলমান সম্বন্ধে যে প্রকার উক্তি করেন না, তিনি লক্ষ্মণসেন সম্বন্ধে তাহাও করিয়াছেন। তিনি তাঁহাকে “সুলতান করিম কুতবুদ্দীন হাতেমুজ্জামান” বা সেই যুগের হাতেম কুতবুদ্দীনের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছেন যেন তিনি “পরলোকে লক্ষ্মণসেনের শাস্তির (যাহা অমুসলমান মাত্রেরই প্রাপ্য) লাঘব করেন।”
সুতরাং মীনহাজুদ্দিনের উক্তি সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেও লক্ষ্মণসেনের চরিত্র ও খ্যাতি সম্বন্ধে উচ্চ ধারণাই পোষণ করিতে হয়। বখতিয়ার কর্ত্তৃক নদীয়া অধিকারের জন্য যে বৃদ্ধ রাজা অপেক্ষা তাঁহার মন্ত্রী, সৈন্যাধ্যক্ষগণ ও প্রজাবৰ্গই অধিকতর দায়ী যে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকিতে পারে না। যিনি আকৌমার যুদ্ধক্ষেত্রে শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, গৌড়, কামরূপ, কলিঙ্গ, বারাণসী ও প্রয়াগে যাঁহার বীরত্ব খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল, মীনহাজুদ্দিনের লেখনী তাঁহার পূত চরিত্রে কলঙ্ক কালিমা লেপন করে নাই।
কিন্তু মীনহাজুদ্দিনের নদীয়া অভিযান কাহিনী সম্পূর্ণরূপে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। যে বিশ্বাসী লোকেরা তাঁহাকে সংবাদ যোগাইয়াছিল, তাহাদের জ্ঞান ও বুদ্ধি কত দূর ছিল, তাহা লক্ষ্মণসেনের অদ্ভুত জন্মবিবরণ ও তাঁহার ৮০ বৎসর রাজত্বের কথা হইতেই বুঝা যায়। বিশেষত এই কাহিনীর মধ্যে অনেক সুপরিচিত প্রবাদ, কথা ও অবিশ্বাস্য ঘটনার সমাবেশ আছে। ‘তুরস্ক আক্রমণ সম্বন্ধে হিন্দুর শাস্ত্রবাণী’ চচ্নামা নামক গ্রন্থে সিন্ধুদেশ সম্বন্ধেও উল্লিখিত হইয়াছে। এই শাস্ত্রবাণীর মূল্য যাহাই হউক, ইহাতে প্রমাণিত হয় যে নদীয়া আক্রমণের অন্তত এক বৎসর পূর্ব্বে ইহার সম্ভাবনা রাজকর্ম্মচারীরা জ্ঞাত ছিলেন। অথচ বখতিয়ার বিহার হইতে নদীয়া পৌঁছিলেন, ইহার মধ্যে তাঁহার অভিযানের কোনো সংবাদ সেন রাজদরবারে পৌঁছিল না। যে সময় তুরস্ক সেনা কর্ত্তৃক দেশ আক্রান্ত হইবার পূর্ণ সম্ভাবনা বিদ্যমান, সেই সময়ে রাজধানীর দ্বাররক্ষাকারীরা ১৮ জন অশ্বারোহী তুর্কীকে বিনা বাধায় নগরে প্রবেশ করিতে দিল এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত বর্ম্মাবৃত সৈন্যকে অশ্বব্যবসায়ী বলিয়া ভুল করিল; নগররক্ষীরাও কোনো সন্দেহ করিল না এবং বখতিয়ার বিনা বাধায় রাজপ্রাসাদের তোরণ পৰ্য্যন্ত পৌঁছিলেন; যখন বখতিয়ারের অবশিষ্ট সৈন্যদল নগরে প্রবেশ করিল তখনো এই অগ্রগামী ১৮ জন অশ্বারোহীকে সন্দেহ করিয়া কেহ তাহাদের গতি প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হইল না! রাজার দেহরক্ষী বা সৈন্যদল অবশ্যই ছিল; এবং যখন রাজা স্বয়ং নদীয়াতে ছিলেন তখন অন্তত একদল রাজসৈন্য তাঁহার রক্ষাকার্যে নিযুক্ত ছিল; অথচ বখতিয়ারের সৈন্যদলের কাহারও গায়ে একটি আঁচড় লাগিল না, তাহারা স্বচ্ছন্দে বিনা বাধায় হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠনকার্য চালাইতে লাগিল। এ সমুদয় এতই অস্বাভাবিক যে খুব দৃঢ় বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ ব্যতীত সত্য বলিয়া স্বীকার করা অসম্ভব।
অথচ যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া মীনহাজুদ্দিন এই অদ্ভুত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা খুবই অকিঞ্চিৎকর। একজন অতিবৃদ্ধ সৈনিক তাঁহাকে বিহার অভিযানের কাহিনী শুনাইয়াছিল। নদীয়া অভিযানের সম্বন্ধে কোনো লিখিত দলিল বা বিবরণ তিনি পান নাই। যে এই কাহিনী বলিয়াছিল তাঁহার এই অভিযানের সম্বন্ধে কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থাকিলে মীনহাজুদ্দিন তাহা উল্লেখ করিতেন। সুতরাং লক্ষ্মণাবতীর বাজারে প্রচলিত নানাবিধ জনপ্রবাদের উপরই এই কাহিনী প্রতিষ্ঠিত এই অনুমান অসঙ্গত নহে। যে সময়ে মীনহাজুদ্দিন এই কাহিনী শুনিয়াছিলেন তখন অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ তুর্কীদের রাজ্য আৰ্যাবর্তে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং একে একে প্রাচীন হিন্দুরাজ্য তাহাদের পদানত হইয়াছে। বিজয়গৰ্ব্বে দৃপ্ত, প্রভুত্বের উন্মাদনায় মত্ত, বিজিত পরাধীন জাতির প্রতি হতশ্রদ্ধ সাধারণ তুরস্ক সৈনিক অথবা রাজপুরুষ যে নিজেদের অতীত জয়ের ইতিহাস অতিশয়োক্তি ও অলৌকিক কাহিনী দ্বারা রঞ্জিত করিবে ইহা খুব স্বাভাবিক। নদীয়া জয়ের সম্বন্ধে মীনহাজুদ্দিনের বিবরণ ছাড়া আরও অনেক অদ্ভুত কাহিনী প্রচলিত ছিল। মীনহাজুদ্দিনের গ্রন্থরচনার অনধিক এক শতাব্দী পরে (১৩৫০ অব্দে) ঐতিহাসিক ইসমী তাঁহার ফুতু-উস-সলাটিন গ্রন্থে লিখিয়াছেন: “মুহম্মদ বখতিয়ার বণিকের ন্যায় সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেন। রাজা লখমনিয়া শুনিলেন যে একজন সওদাগর বহু মূল্যবান দ্রব্যজাত ও তাতার দেশীয় অশ্ব বিক্রয় করিতে তাঁহার রাজধানীতে আসিয়াছে। লক্ষ্মণসেন রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়া দ্রব্যগুলি ক্রয় করিবার জন্য সওদাগরের নিকট গেলেন। বখতিয়ার রাজাকে দ্রব্য দেখাইতেছেন এমন সময় পূৰ্ব্বব্যবস্থামতো তাঁহার ইঙ্গিতে তাঁহার অনুচরগণ সহসা চতুর্দিক হইতে হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিল। অতর্কিত আক্রমণে হিন্দুরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল কিন্তু রাজার দেহরক্ষীগণ বহুক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিল। খিলজী বীরগণ অল্পসংখ্যক রক্ষীগণকে হত্যা করিয়া রাজাকে বন্দী করিয়া বখতিয়ারের নিকট লইয়া গেলেন। বখতিয়ার ঐ রাজ্যের রাজা হইলেন।”
এই কাহিনীর সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। মীনহাজুদ্দিনের কাহিনী যে সে যুগেও সকলে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করে নাই ইহা তাঁহার একটি প্রমাণ। কারণ তাহা হইলে অব্যবহিত পরবর্ত্তী অপর একজন ঐতিহাসিক তাঁহার উল্লেখমাত্র না করিয়া এইরূপ অদ্ভুত আখ্যানের অবতারণা করিতেন না। ইহা হইতে আরও প্রমাণিত হয় যে বখতিয়ার কর্ত্তৃক লক্ষ্মণসেনের পরাজয় সম্বন্ধে কোনো বিশ্বস্ত বিবরণ ঐতিহাসিকগণের জানা ছিল না, এবং এ সম্বন্ধে বিবিধ আজগুবি কাহিনীর সৃষ্টি হইয়াছিল। মীনহাজুদ্দিন ও ইসমী দুইটি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, এবং সম্ভবত এরূপ আরও অনেক গল্প প্রচলিত ছিল।
কেহ কেহ মীনহাজুদ্দিনের বিবরণ একেবারে অমূলক বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সঙ্গত বোধ হয় না। মোটের ওপর মীনহাজুদ্দিনের উক্তি হইতে এই সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণসেন যখন নদীয়ায় বাস করিতেছিলেন তখন বখতিয়ার খিলজী তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্য এক ক্ষুদ্র অশ্বারোহী সৈন্যদল লইয়া বিহার হইতে দ্রুতগতিতে অপ্রত্যাশিত পথে আসিয়া অতর্কিতে ঐ নগরী আক্রমণ করেন, এবং রাজাকে না পাইয়া ঐ নগরী লুণ্ঠন করিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। নদীয়া তখন সেনদের প্রধান রাজধানী অথবা বিশেষভাবে সুরক্ষিত ছিল কি না তাহা নিশ্চিত জানিবার উপায় নাই।
বখতিয়ার যে নদীয়ায় বসতি করেন নাই, বরং ইহা ধ্বংস করিয়াছিলেন, মীনহাজুদ্দিন তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার নদীয়া আক্রমণ গৌড় জয়ের প্রথম অভিযান কি না তাহাও নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। মীনহাজুদ্দিন লিখিয়াছেন যে বিহার জয়ের পূর্ব্বে তিনি ঐ প্রদেশের নানা স্থানে লুটতরাজ করিয়া ফিরিতেন। “কিল্লা বিহারের” ন্যায় কেবলমাত্র লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যেই তিনি অতর্কিত নদীয়া আক্রমণ করিয়া থাকিবেন ইহাও অসম্ভব নহে।
১২৫৫ অব্দে মুঘিসুদ্দিন উজবেক নদীয়া জয়ের চিহ্নস্বরূপ যে মুদ্রা প্রচলিত করেন তাহা হইতে অনুমিত হয় যে ঐ তারিখের পূৰ্ব্বে নদীয়ায় তুর্কী শাসন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং নদীয়া কিছুদিন বখতিয়ারের অধিকারে থাকিলেও ইহা যে আবার সেন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল এরূপ অনুমান করাই সঙ্গত।
নদীয়া জয়ের কত দিন পরে এবং কিভাবে বখতিয়ার লক্ষ্মণাবতী জয় করিয়া সেখানে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন মীনহাজুদ্দিনের গ্রন্থে তাঁহার কোনো উল্লেখ নাই। লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার বংশধরেরা নদীয়া জয়ের পর বহু বৎসর বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি এবং তাঁহার দুই পুত্র যে ম্লেচ্ছ ও যবনদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন সমসাময়িক তাম্রশাসন ও কবিতায় তাঁহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। যখন প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত তুর্কীগণের পদানত, তখনো যাঁহারা বীরবিক্রমে বঙ্গের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সৈন্যবল এত দুৰ্বল বা শাসনতন্ত্র এমন বিশৃঙ্খল ছিল না যে অতর্কিত আক্রমণে নদীয়া অধিকার করিতে পারিলেও বখতিয়ার বিনা বাধায় গৌড় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই গৌড় জয়ের কোনো ঐতিহাসিক বিবরণই পাওয়া যায় নাই।
.
৬. সেন রাজ্যের পতন
আ ১২০২ অব্দে বখতিয়ার নদীয়া আক্রমণ করেন। ইহার পরও লক্ষ্মণসেন অন্তত তিন-চারি বৎসর রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার এই সময়কার দুইখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে রাজকবি যেভাবে তাঁহার শৌর্যবীর্যের ও প্রাচীন রীতি অনুযায়ী রাজপদবী প্রভৃতির উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে বাংলা দেশের গুরুতর রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের কোনো আভাসই পাওয়া যায় না। অপরদিকে উত্তরবঙ্গ অথবা তাঁহার এক অংশ ব্যতীত বখতিয়ার বাংলার আর কোনো প্রদেশে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিলেন ইহার কোনো প্রমাণ নাই। বঙ্গজয় সম্পূর্ণ না করিয়াই বখতিয়ার সুদূর তিব্বতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং এই অভিযানে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করেন। বখতিয়ারের এই বিফলতার সহিত সেনরাজগণের যুদ্ধোদ্যমের কোনো সম্বন্ধ আছে কি না তুর্কী ঐতিহাসিকগণ সে সম্বন্ধে একেবারে নীরব।
লক্ষ্মণসেন ও বখতিয়ার উভয়েই সম্ভবত ১২০৫ অব্দে বা তাঁহার দুই-এক বৎসরের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। লক্ষ্মণসেনের পর তাঁহার দুই পুত্র বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন। সম্ভবত বিশ্বরূপসেনই জ্যেষ্ঠ ছিলেন এবং প্রথমে রাজত্ব করেন, কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা যায়। এই দুই রাজারই তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে বিশ্বরূপসেন “অরিরাজ বৃষভাঙ্কশঙ্কর গৌড়েশ্বর” ও কেশবসেন “অরিরাজ অসহ্য শঙ্কর গৌড়েশ্বর উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। উভয়েই ‘সৌর’ অর্থাৎ সূর্যের উপাসক ছিলেন। এইরূপে দেখা যায় যে, সেনরাজগণ যথাক্রমে শৈব, বৈষ্ণব ও সৌর সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছিলেন।
এই দুই রাজার রাজ্যকালের কোনো বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু দক্ষিণ ও পূৰ্ব্ব বাংলা যে তাঁহাদের রাজ্যভুক্ত ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কারণ ইহাদের তাম্রশাসনে বিক্রমপুর ও দক্ষিণবঙ্গের সমুদ্রতীরে ভূমিদানের উল্লেখ আছে। বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন উভয়েই “যবনান্বয়-প্রলয়-কাল-রুদ্র” বলিয়া তাম্রশাসনে অভিহিত হইয়াছেন। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে উভয়েই উত্তরবঙ্গের মুসলমান তুর্কীরাজ্যের সহিত যুদ্ধে সফলতা লাভ করিয়াছিলেন। ইহা কেবলমাত্র প্রশস্তিকারের স্তুতিবাক্য নহে। কারণ মীনহাজুদ্দিনের ইতিহাস হইতেও প্রমাণিত হয় যে তুর্কীগণ উত্তরবঙ্গের সমগ্র অথবা অধিকাংশ অধিকার করিলেও বহুদিন পৰ্য্যন্ত পূৰ্ব্ব ও দক্ষিণবঙ্গ অধিকার করিতে পারেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন যে গঙ্গার দুই তীরে, রাঢ় ও বরেন্দ্রেই, তুর্কীরাজা সীমাবদ্ধ ছিল, এবং তখনো লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ বঙ্গে রাজত্ব করিতেন। তুর্কীরাজগণ যে মধ্যে মধ্যে বঙ্গে অভিযান করিতেন তাহাও এই গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন যে যবণ-রাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পূৰ্ব্ব ও দক্ষিণবঙ্গ স্বীয় অধিকারে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।
বিশ্বরূপসেনের একখানি তাম্রশাসন তাঁহার রাজত্বের চতুর্দ্দশ সম্বৎসরে এবং আর একখানি ইহার পরে প্রদত্ত হইয়াছিল। কেশবসেনের তাম্রশাসনখানির তারিখ তাঁহার রাজ্যের তৃতীয় বৎসর। সুতরাং এই দুই ভ্রাতার মোট রাজ্যকাল প্রায় ২৫ বৎসর ছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। কেশবসেনের মৃত্যুর পরে (আ ১২৩০) কে রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না। বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে কুমার সূৰ্য্যসেন ও কুমার পুরুষোত্তমসেনের নামোল্লেখ আছে। কুমার’ এই উপাধি হইতে অনুমিত হয় যে ইহারা উভয়েই রাজপুত্র, অন্তত রাজবংশীয়, ছিলেন। কিন্তু ইহাদের কেহ যে রাজা হইয়াছিলেন তাঁহার প্রমাণ নাই। পরবর্ত্তীকালে রচিত রাজাবলী, বিপ্রকল্পলতিকা প্রভৃতি গ্রন্থ, আবুল ফজল প্রণীত আইন-ই-আকবরী এবং এদেশে প্রচলিত লৌকিক কাহিনীতে অনেক সেনরাজার নামোল্লেখ আছে, কিন্তু এই সমুদয় বিবরণ ঐতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। মীনহাজুদ্দিনের পূৰ্বোল্লিখিত উক্তি হইতে প্রমাণিত হয় যে তিনি যে সময়ে তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করেন (আ ১২৬০ অব্দ),-অন্তত যে সময়ে লক্ষ্মণাবতীতে আসিয়া বাংলা দেশের ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করেন (আ ১২৪৪ অব্দ)-তখনো লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ বঙ্গে রাজত্ব করিতেন। সুতরাং কেশবসেনের পরেও যে এক বা একাধিক সেন রাজা বঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই।
‘পঞ্চরক্ষা’ নামক একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থের পুঁথি হইতে জানা যায় যে, ইহা ১২১১ শকে (১২৮৯ অব্দে) পরমসৌগত পরমরাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর মধুসেনের রাজ্যে লিখিত হইয়াছিল। এই বৌদ্ধ নরপতি মধুসেন লক্ষ্মণসেনের বংশধর কি না তাহা সঠিক জানা যায় না, কিন্তু তাঁহার ‘সেন’ উপাধি হইতে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। মধুসেন এয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্যের অবস্থিতি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তিনি গৌড়েশ্বর উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু গৌড়ের কোনো অংশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল কি না অন্য সমর্থক প্রমাণ না পাইলে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যা না। মুধুসেনের পর বাংলায় সেন উপাধিধারী কোনো রাজার অস্তিত্বের প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। বর্দ্ধমান জিলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত মঙ্গলকোট নামক গ্রামের এক মসজিদে একখানি ভগ্ন প্রস্তরখণ্ডে একটি সংস্কৃত লিপির কিয়দংশ উত্তীর্ণ আছে। কেহ কেহ বলেন ইহাতে চন্দ্রসেন নামক রাজার উল্লেখ আছে। কিন্তু এই রাজার সম্বন্ধে আর কোনো বিবরণ জানা যায় নাই।
এয়োদশ শতাব্দীতে বুদ্ধসেন ও তাঁহার পুত্র জয়সেন পীঠি রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। বর্ত্তমান গয়া জিলায় পীঠি রাজ্য অবস্থিত ছিল। পীঠিপতি আচাৰ্য্য জয়সেন “লক্ষ্মণসেনস্য অতীতরাজ্য-সম্বৎসর-৮৩” এই অব্দে বৌদ্ধগয়ার মহাবোধি বিহারকে একখানি গ্রাম দান করেন। এই তারিখের প্রকৃত অর্থ লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। “লক্ষ্মণসেনের রাজ্য ধ্বংস হওয়ার ৮৩ বৎসর পরে,”-উক্ত পদের এই প্রকার অর্থই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। গয়া অঞ্চলে আ ১২০০ অব্দে সেনরাজ্য ধ্বংস হয়। সুতরাং বুদ্ধসেন ও জয়সেন ত্রয়োদশ শতাব্দের শেষার্ধে রাজত্ব করিতেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে তুরস্ক বিজয়ের পরও মগধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য বিদ্যমান ছিল এবং সেন উপাধিধারী রাজগণ তথায় রাজত্ব করিতেন।
তিব্বতীয় লামা তারনাথ লিখিয়াছেন যে সেনবংশীয় লবসেন, কাশসেন, মণিতসেন এবং রাথিকসেন এই চারিজন রাজা মোট ৮০ বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপর লবসেন, বুদ্ধসেন, হরিতসেন এবং প্রতীতসেন এই চারিজন তুরস্ক রাজার অধীনে রাজত্ব করেন। তারনাথের এই উক্তির সমর্থক কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু অসম্ভব নহে যে তারনাথ কথিত বুদ্ধসেনই পূর্ব্বোক্ত পীঠিপতি বুদ্ধসেন।
পীঠির সেনরাজগণের সহিত বাংলার সেনরাজবংশের কোনো সম্বন্ধ ছিল কি না তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। জয়সেনের লিপিতে লক্ষ্মণসেনের নাম সংযুক্ত সম্বৎসর ব্যবহৃত হওয়ায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে এককালে এই অঞ্চল লক্ষ্মণসেনের রাজ্যভুক্ত ছিল কিন্তু ইহা হইতে জয়সেনের সহিত লক্ষ্মণসেনের কোনো বংশগত সম্বন্ধ ছিল এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। তবে এরূপ সম্বন্ধ থাকা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব নহে।
পঞ্জাবের অন্তর্গত সুকে, কেওস্থল, কষ্টওয়ার এবং মণ্ডী প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য রাজ্যের রাজাদের মধ্যে একটি প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত আছে যে তাঁহাদের পূৰ্বপুরুষগণ গৌড়ের রাজা ছিলেন। এই সমুদয় রাজাদের সেন উপাধি হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, হঁহারা বাংলার সেনরাজগণের বংশধর। অবশ্য সমর্থক অন্য প্রমাণ না পাইলে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্ত করা যায় না।
তুর্কী আক্রমণই সেন রাজবংশের পতনের একমাত্র কারণ নহে। সম্ভবত আভ্যন্তরিক বিদ্রোহও ইহার ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিয়াছিল। ডোম্মনপাল দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সুন্দরবন অঞ্চলে যে এক স্বাধীন রাজ্যের পত্তন করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তুর্কী আক্রমণের ফলে সেনরাজগণের বিপদ ও দুর্বলতার সুযোগে এইরূপ আরও কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।
সেনরাজগণের রাজধানী কোথায় ছিল সে সম্বন্ধে এ যাবৎ বহু বাদানুবাদ হইয়াছে। ইহার বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। রাঢ় দেশের কোন অংশে হেমন্ত সেন রাজত্ব করিতেন এবং তাঁহার রাজধানী কোথায় ছিল তাহা বলা যায় না। কিন্তু বিজয়সেন বঙ্গদেশ জয় করার পর যে ঢাকার নিকটবর্ত্তী বিক্রমপুরে সেনরাজগণের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। বিজয়সেন ও বল্লালসেনের এবং লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের প্রথমভাগের যে সমুদয় তাম্রশাসন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাঁহার সকলই “শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার” হইতে প্রদত্ত। “স্কন্ধাবার” শব্দে শিবির ও রাজধানী উভয়ই বুঝায়, কিন্তু যখন তিনজন রাজার তাম্রশাসনেই এই এক স্কন্ধাবারের উল্লেখ পাওয়া যায়, তখন ইহাকে রাজধানী অর্থেই গ্রহণ করা সঙ্গত। ইহার অন্যবিধ প্রমাণও আছে। বিজয়সেনের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তাঁহার মহাদেবী অর্থাৎ প্রধানা মহিষী বিলাসদেবী বিক্রমপুর উপকারিকা মধ্যে তুলাপুরুষ মহাদান নামক বিরাট অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। সুতরাং বিক্রমপুর যে অস্থায়ী শিবির মাত্র নহে, কিন্তু স্থায়ী রাজধানী ছিল, সে বিষয় সন্দেহ নাই। এখনো স্থানীয় প্রবাদ অনুসারে বিক্রমপুরে বল্লালবাড়ী প্রভৃতি সেনরাজগণের অতীত কীৰ্ত্তির ধ্বংসপ্রাপ্ত নিদর্শন আছে।
লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষভাগে উৎকীর্ণ দুইখানি তাম্রশাসন ধার্যগ্রাম, ও তাঁহার দুই পুত্রের তাম্রশাসন ফল্পগ্রাম স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত। ধাৰ্য্যগ্রাম ও ফরুগ্রামের অবস্থিতি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার পুত্রগণ বিক্রমপুর পরিত্যাগ করিয়া এই দুই স্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন কি না তাহাও নিশ্চিত বলা যায় না।
অনুমিত হয় যে পালরাজগণের ন্যায় সেনরাজগণেরও একাধিক রাজধানী ছিল। লক্ষ্মণসেনের সময় অথবা তাঁহার পূৰ্ব্বে সম্ভবত গৌড় ও নদীয়ায় সেনরাজগণের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। কারণ মুসলমান ইতিহাস গৌড় লক্ষ্মণাবতী নামে পরিচিত এবং সম্ভবত লক্ষ্মণসেনের নাম অনুসারেই গৌড়ের এই নাম পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। মীনহাজুদ্দিনের বর্ণনা অনুসারে মহম্মদ বখতিয়ারের আক্রমণের সময় লক্ষ্মণসেন রাজধানী নদীয়ায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। বাংলার কুলজী গ্রন্থ অনুসারে বল্লালসেন বৃদ্ধবয়সে রাজধানী নবদ্বীপে বাস করিতেন। বল্লালচরিতে উক্ত হইয়াছে যে বল্লালসেনের তিনটি রাজধানী ছিল বিক্রমপুর, গৌড় ও স্বর্ণগ্রাম। কবি ধোয় রচিত পবনদূত কাব্যে গঙ্গাতীরবর্ত্তী বিজয়পুর নগরী লক্ষ্মণসেনের রাজধানীরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই বিজয়পুরের অবস্থিতি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বিজয়পুরকে নদীয়ার সহিত অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, আবার কাহারও মতে রাজসাহীর অন্তর্গত রামপুর বোয়ালিয়ার দশ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত বিজয়নগর গ্রামই প্রাচীন বিজয়পুর; কিন্তু পবনদূতে ত্রিবেণী সঙ্গমের পরই বিজয়পুরের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং গঙ্গা নদী পার হইবার কোনো প্রসঙ্গ নাই, সুতরাং বর্ত্তমান নদীয়াই প্রাচীন বিজয়পুর এই মতটিই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। সম্ভবত বিজয়সেনের নাম অনুসারেই এই নামকরণ হইয়াছিল।
১৩. পাল ও সেনরাজগণের কাল-নির্ণয়
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ –পাল ও সেনরাজগণের কাল-নির্ণয়
পাল ও সেনরাজগণের কাল-নির্ণয় লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এ স্থলে সম্ভবপর নহে। তবে যে প্রণালীতে এই গ্রন্থে এই সমুদয় কাল-নির্ণয় করা হইয়াছে তাঁহার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।
পালরাজগণের মধ্যে কেবলমাত্র প্রথম মহীপালের সারনাথ লিপিতে একটি নির্দিষ্ট তারিখের উল্লেখ আছে-১০৮৩ সম্বৎ অর্থাৎ ১০২৬ খৃষ্টাব্দ। মহীপাল এই তারিখে রাজত্ব করিতেন ইহা ধরিয়া লইয়া, তাঁহার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী রাজগণের মোট রাজত্বকাল যত দূর জানা আছে তাঁহার সাহায্যে মোটামুটিভাবে পালরাজগণের কাল নির্ণয় করা যায়। তারপর পালরাজগণের সমসাময়িক অন্যান্য যে সমুদয় ভারতীয় রাজগণের তারিখ সঠিক জানা আছে, তাঁহার সাহায্যে এই কাল নির্ণয় আরও একটু সংকীর্ণভাবে করা সম্ভবপর। ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের, মহীপাল রাজেন্দ্ৰচোলের এবং নয়পাল কলচুরি কর্ণের সমসাময়িক ছিলেন ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এবং সৌভাগ্যের বিষয় এই সমুদয় বিদেশী রাজগণের তারিখও সঠিকভাবে জানিবার উপায় আছে। এই সমুদয় আলোচনাপূর্ব্বক পালরাজগণের নিম্নলিখিত কাল নির্ণয় করা হইয়াছে।
রাজার নাম –মোট জানা রাজত্বকাল –রাজ্যলারে আনুমানিক অব্দ
১। গোপাল (১ম) –X –৭৫০
২। ধর্ম্মপাল –৩২ –৭৭০
৩। দেবপাল –৩৯ (অথবা ৩৫) –৮১০
৪। বিগ্রহপাল অথবা (১ম) শূরপাল – ৩ –৮১০
৫। নারায়ণপাল – ৫৪ –৮৫৪
৬। রাজ্যপাল – ৩২ –৯০৮
৭। গোপাল (২য়) –১৭ –৯৪০
৮। বিগ্রহপাল (২য়) –২৬ (?) –৯৬০
৯। মহীপাল (১ম) – ৪৮ –৯৮৮
১০। নয়পাল – ১৫ –১০৩৮
১১। বিগ্রহপাল (৩য়) – X –১০৫৫
১২। মহীপাল (২য়) – X -১০৭০
১৩। শূরপাল (২য়) — X –১০৭৫
১৪। রামপাল –৪২ –১০৭৭
১৫। কুমারপাল –X –১১২০
১৬। গোপাল (৩য়) –১৪ –১১২৫
১৭। মদনপাল –১৪ –১১৪০
১৮। গোবিন্দপাল –৪ –১১৫৫
সেনরাজগণের কাল নির্ণয় বিষয়ে দুইটি মূল্যবান উপাদান আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় ইহারা পরস্পরবিরোধী। প্রথমত লক্ষ্মণ সংবৎ (ল সং) নামে একটি অব্দ প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি মিথিলায় প্রচলিত আছে। ১১০৭ হইতে ১১১৯ অব্দের মধ্যে কোনো সময়ে ইহার প্রথম বৎসর গণনা আরম্ভ করা হয়। সাধারণত কোনো রাজার রাজ্যপ্রাপ্তির সময় হইতেই তাঁহার নামে অব্দ প্রচলিত হয়। সুতরাং লক্ষ্মণ সংবতের আরম্ভকালে অর্থাৎ ১১০৭ হইতে ১১১৯ অব্দের মধ্যে লক্ষ্মণসেন রাজ্য লাভ করেন অনেকে এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।
অপরপক্ষে বল্লালসেন রচিত দানসাগর ও অদ্ভুতসাগরের বহুসংখ্যক পুঁথির উপসংহারে স্পষ্ট লিখিত আছে যে ১০৮১ (অথবা) ১০৮২ শাকে (১১৫৯-৬০ অব্দে) বল্লালসেনের রাজ্যারম্ভ, ১০৯১ শাকে (১১৬৯ অব্দ) দানসাগরের রচনাকাল এবং ১০৮৯ (অথবা ১০৯০) শাকে (১১৬৭-৬৮ অব্দ) অদ্ভুতসাগর গ্রন্থের রচনা আরম্ভ হয়। কোনো কোনো পুঁথিতে এই সময়জ্ঞাপক শ্লোকগুলি না থাকায় কেহ কেহ এইগুলির উপর আস্থা স্থাপন করেন না। কিন্তু এযাবৎ যত পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাঁহার প্রায় সকলগুলিতেই এই সমুদয় শ্লোক পাওয়া যায়, যে দুই একখানি পুঁথিতে এই সমুদয় শ্লোক নাই সে পুঁথিতেও গ্রন্থমধ্যে নানা স্থানে উহার কোনো কোনো তারিখের উল্লেখ আছে। রাজা টোডরমলু অদ্ভুতসাগরের পুঁথিতে এই তারিখের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে বল্লালসেন ১১৬০-৬১ অব্দে রাজত্ব করিতেন।
এই সমুদয় তারিখের সমর্থক আর একটি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। লক্ষ্মণসেনের সভাকবি শ্রীধরদাসের সদুক্তিকর্ণামৃত গ্রন্থের পুঁথিতে যে পুস্পিকা আছে তাহা হইতে জানা যায় যে, ১১২৭ শাকে (=১২০৫ অব্দে) লক্ষ্মণসেনের ‘রসৈক-বিংশ’ রাজ্য সম্বৎসরে এই গ্রন্থ রচিত হয়। রসৈক-বিংশ পদের অর্থ ২৭ (রস= ৬+১+২০)। এইরূপ পদের প্রয়োগ একটু অদ্ভুত বলিয়া কেহ কেহ এই পদটিকে রাজ্যৈকবিংশ’ এইরূপ পাঠ করিয়া ১২০৫ অব্দে লক্ষ্মণসেনের একবিংশতি বৎসর রাজ্যকাল এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সে যাহা হইক ১২০৫ অব্দে যে লক্ষ্মণসেন রাজত্ব করিতেন সদুক্তিকর্ণামৃত হইতে তাহা প্রমাণিত হয় এবং এই সিদ্ধান্ত বল্লালসেনের কালজ্ঞাপক পূৰ্ব্বোক্ত শ্লোকগুলির সম্পূর্ণ সমর্থন করে। এই সমুদয়ের উপর নির্ভর করিয়া এই গ্রন্থে সেনরাজগণের নিম্নলিখিতরূপ কাল নির্ণয় করা হইয়াছে এবং পণ্ডিতগণ প্রায় সকলেই এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।
| রাজার নাম | মোট জানা রাজত্বকাল | রাজ্যলাভের আনুমানিক অব্দ |
| বিজয়সেন | ৬২ (৩২) | ১০৯৫ (১১২৫?) |
| বল্লালসেন | ১১ | ১১৫৮ |
| লক্ষ্মণসেন | ২৭ | ১১৭৯ |
| বিশ্বরূপসেন | ১৪ | ১২০৬ |
| কেশবসেন | ৩ | ১২২৫ |
বিজয়সেনের বারাকপুর লিপির তারিখ কেহ ৩২ এবং কেহ ৬২ পাঠ করিয়াছেন। এই দুই ভিন্ন পাঠ গ্রহণ করিলে তাঁহার রাজ্যারম্ভকাল কিরূপ বিভিন্ন হইবে তাহা উপরে বন্ধনীযুক্ত সংখ্যা দ্বারা দেখানো হইয়াছে।
প্রশ্ন উঠিতে পারে যে লক্ষ্মণসেন যদি ১১৭৯ অব্দে রাজ্যলাভ করিয়া থাকেন তবে ১১০৭ হইতে ১১১৯ অব্দের মধ্যে তাঁহার নামযুক্ত লক্ষ্মণ সংবৎ আরম্ভ হইল কিরূপে? এই প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে। তবে এ বিষয়ে কয়েকটি কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। প্রথমত লক্ষ্মণসেনের রাজ্যারম্ভকাল হইতে কোনো অব্দের প্রতিষ্ঠা হইলে বঙ্গদেশে তাঁহার প্রচলন হইত এবং তাঁহার পুত্রদ্বয় বিশ্বরূপসেন এবং কেশবসেনের তাম্রশাসনে তাঁহাদের রাজ্যাঙ্কের পরিবর্তে এই অব্দেরই ব্যবহার হইত, এইরূপ অনুমান সম্পূর্ণ সঙ্গত। দ্বিতীয়ত লক্ষ্মণ সংবতের ব্যবহারের পূর্ব্বে মগধের তিনটি প্রাচীন লিপিতে নিম্নলিখিতরূপে তারিখ দেওয়া হইয়াছে।
১। শ্রীমল্লখণসেনস্যাতীতরাজ্যে সং ৫১
২। শ্রীমল্ললক্ষ্মণসেনদেবপাদানামতীতরাজ্যে সং ৭৪
৩। লক্ষ্মণসেনস্যাতীতরাজ্যে সং ৮৩
পালবংশীয় (অথবা পাল-উপাধিধারী) শেষ রাজা গোবিন্দপালের নাম সংযুক্ত এইরূপ তারিখ একখানি শিলালিপি ও কয়েকখানি পুঁথিতে পাওয়া যায় যথা :
১। শ্রীগোবিন্দপালদেবগতরাজ্যে চতুর্দ্দশসম্বৎসরে
২। শ্রীমদৃগোবিন্দপালদেবানাং বিনষ্টরাজ্যে অষ্টত্রিংশৎসম্বৎ
এই সমুদয় পদের প্রকৃত ব্যাখ্যা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। কিন্তু এই সমুদয় তারিখ যে গোবিন্দপাল ও লক্ষ্মণসেনের রাজ্য শেষ হইতে গণনা আরম্ভ হইয়াছে তাহাই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। সাধারণত কোনো রাজার রাজ্যকালে কোনো লিপি বা পুঁথি লিখিত হইলে তাঁহার ‘প্রবর্দ্ধমান-বিজয়রাজ্য-সংবৎসরে’ দিয়া তারিখ দেওয়া হইত। কিন্তু বৌদ্ধ পাল বংশ ধ্বংস হইলে বৌদ্ধবিহারের ভিক্ষুগণ নবাগত হিন্দু রাজার প্রবর্দ্ধমান বিজয়রাজ্যের পরিবর্তে বৌদ্ধ রাজবংশের ধ্বংস হইতেই তারিখ গণনা করিতেন, এবং মগধ মুসলমান বিজেতার পদানত হইলে মগধবাসীগণ মুসলমান রাজার প্রবর্দ্ধমান বিজয়রাজ্যের পরিবর্তে শেষ হিন্দুরাজা লক্ষ্মণসেনের রাজ্যশেষ হইতে তারিখ গণনা করিতেন-ইহাই উক্ত তারিখযুক্ত পদগুলি হইতে অনুমান হয়। সুতরাং প্রথমে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যধ্বংস হইতেই একটি অব্দের গণনা আরম্ভ হয়। বাংলায় প্রচলিত বলালি সন ও পরগণাতি সনও ঐ অব্দ বলিয়াই অনুমিত হয়। কারণ এ উভয়ই ১২০০ খৃষ্টাব্দের দুই-এক বৎসর আগে বা পরে আরম্ভ হইয়াছে।
এই অব্দ কিছুকাল প্রচলিত থাকিবার পর সম্ভবত মিথিলায় লক্ষ্মণসেনের রাজ্যধ্বংসের পরিবর্তে তাঁহার জন্ম হইতে এক অব্দ গণনার রীতি প্রবর্তিত হয় এবং এই জন্মতারিখ হইতে গণনা করিয়া লক্ষ্মণ সংবৎ প্রচলিত হয়। মীনহাজুদ্দিন লিখিয়াছেন যে বখতিয়ারের আক্রমণকালে লক্ষ্মণসেনের বয়স প্রায় ৮০ বৎসর হইয়াছিল। এই উক্তি অনুসারে আ ১১১৯ অব্দে লক্ষ্মণসেনের জন্ম হইয়াছিল। লক্ষ্মণ সংবতের সহিত শকাব্দ ও সংবতের তারিখ দেওয়া আছে এরূপ বহু দৃষ্টান্ত আলোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে ‘লসং’-এর আরম্ভকাল ১১০৭ হইতে ১১১৯ অব্দের মধ্যে বিভিন্ন বৎসরে পড়ে। বর্ত্তমানকালে মিথিলায় যে পঞ্জিকা প্রচলিত আছে তদানুসারে লসং ১১০৮ অব্দে আরম্ভ হইয়াছিল। এই প্রকার বৈষম্যের কারণ কী তাহা জানা যায় নাই। সম্ভবত যখন লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর শতাধিক বর্ষ পরে তাঁহার জন্মতারিখ হইতে লসং গণনা আরম্ভ হয় তখন মিথিলায় এই তারিখটি সঠিক জানা ছিল না এবং এ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত ছিল। সেই জন্যই লসং’ এর বিভিন্ন আরম্ভকালের মধ্যে অনধিক বারো বৎসরের প্রভেদ হইয়াছে। অবশ্য এ সকলই অনুমান মাত্র। লসং-এর প্রকৃত আরম্ভকাল এবং ইহা কোন ঘটনার স্মৃতি বহন করিতেছে তাহা সঠিক জানিবার উপায় নাই। তবে ইহা এক প্রকার স্থির যে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম বা দ্বিতীয় দশকে-যখন হইতে ‘লসং’-এর প্রথম বৎসর গণনা করা হয়-লক্ষ্মণসেন রাজ্য লাভ করেন নাই, সুতরাং লক্ষ্মণসেনের রাজসিংহাসনে আরোহণ উপলক্ষে বা সেই ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য লক্ষ্মণ সংবতের প্রচলন হইয়াছিল এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নহে।
১৪. বাংলার শেষ স্বাধীন রাজ্য
১৪. চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ –বাংলার শেষ স্বাধীন রাজ্য
১. দেববংশ
লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের শেষভাগে মেঘনার পূর্ব্বতীরের মধুমথনদেব একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। মধুমথনদেবের পিতা পুরুষোত্তম ‘দেবাম্বয়-গ্রামণী’ অর্থাৎ দেববংশের প্রধান বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন, কিন্তু এই বংশের কোনো তাম্রশাসনেই তাঁহার সম্বন্ধে রাজপদবীজ্ঞাপক কোনো উপাধি ব্যবহৃত হয় নাই। মধুমথনদেব ও তাঁহার পুত্র বাসুদেব সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। কিন্তু বাসুদেবের পুত্র দামোদরদেবের দুইখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, তিনি ১২৩১ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অন্তত ১২৪৩ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই তাম্রশাসনদ্বয় হইতে অনুমিত হয় যে দামোদরদেবের রাজ্য বর্ত্তমান ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জিলায় সীমাবদ্ধ ছিল। সকল ‘ভূপাল চক্রবর্ত্তী’ ও ‘অরিরাজ-চাণুর-মাধব’ এই উপাধিদ্বয় হইতে অনুমিত হয় যে দামোদর পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। সম্ভবত সেনবংশীয় রাজা বিশ্বরূপসেনের মৃত্যুর পর তিনি পৈত্রিক রাজ্যের সীমা বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।
দামোদরদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্যের কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু ঢাকা জিলার আদাবাড়ী নামক স্থানে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসনে দেব উপাধিধারী আর এক রাজার নাম পাওয়া যায়। এই তাম্রশাসনখানি অতিশয় জীর্ণ এবং ইহার সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার সম্ভব হয় নাই। যেটুকু পড়া গিয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ অরিরাজ-দনুজমাধব দশরথদেব বিক্রমপুর রাজধানী হইতে এই তাম্রশাসন দান করিয়াছিলেন। কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেনের অনুকরণে তিনি অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি, রাজত্রয়াধিপতি উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, এবং সেনরাজগণের “সেনকুল-কমল বিকাস-ভাস্কর” পদবীর পরিবর্তে তাঁহার শাসনে “দেবাম্বয়-কমল-বিকাস-ভাস্কর” ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং তিনি যে দেশবংশীয় ও এই দেববংশ যে অভিন্ন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না।
দশরথদেবের উপাধিদৃষ্টে সহজেই অনুমিত হয় যে সেনবংশীয় শেষ রাজগণের অনতিকাল পরেই তিনি রাজত্ব করেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ অন্তত ১২৪৫ অথবা ১২৬০ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সম্ভবত ইহার পর কোনো সময়ে দশরথদেব সেনরাজগণের রাজ্য অধিকার করিয়া থাকিবেন। তাঁহার তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে যে তিনি নারায়ণের কৃপায় গৌড় রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মতে গৌড় এই সময়ে তুরস্ক রাজগণের অধীনে ছিল। তবে তুরস্ক নায়কগণের গৃহবিবাদের সুযোগে দশরথদেব গৌড়ের কিয়দংশ অধিকার করিয়া কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন ইহা একেবারে অবিশ্বাস্য বলা যায় না। বাংলা দেশে তুরস্ক প্রভুত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে বহুদিন লাগিয়াছিল, এবং এই সময়ের মধ্যে যে হিন্দুরাজগণ লুপ্ত রাজ্য উদ্ধার করিতে পুনঃপুন চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং আংশিকভাবে কৃতকাৰ্য্য হইয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। জিয়াউদ্দিন বার্ণীর ইতিহাসে কথিত হইয়াছে যে দিল্লীর সুলতান গিয়াসুদ্দিন বলবন যখন তুঘরিল খানের বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য বঙ্গদেশে অভিযান করেন তখন সোনারগাঁয়ের রাজা দনুজরায়ের সহিত তাঁহার এইরূপ এক চুক্তিপত্র হয় যে তুঘরিল যাহাতে জলপথে পলায়ন করিতে না পারে দনুজরায় তাঁহার ব্যবস্থা করিবেন। অনেকে অনুমান করেন যে এই দনুজরায় ও অরিরাজ-দনুজমাধব দশরথ অভিন্ন। সোনারগাঁ ও বিক্রমপুর বর্ত্তমানে ধলেশ্বরী নদীর তীরে অবস্থিত। সুতরাং বিক্রমপুরের দিনুজমাধব’ উপাধিধারী রাজা বিদেশী ঐতিহাসিক কর্ত্তৃক সোনারগাঁয়ের রাজা দনুজরায় রূপে অভিহিত হইবেন ইহা খুব অস্বাভাবিক নহে। বাংলার কুলজী গ্রন্থেও দেখিতে পাওয়া যায় যে কেশবসেনের অনতিকাল পরে দনুজমাধব নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। দশরথদেব ও দনুজরায়কে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হয় যে দশরথদেব বলবনের অভিযান সময়ে অর্থাৎ ১২৮৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আসীন ছিলেন।
শ্রীহট্টের নিকটবর্ত্তী ভাটেরা গ্রামে প্রাপ্ত দুইখানি তাম্রশাসন হইতে দেববংশীয় কয়েকজন রাজার বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁহাদের বংশতালিকা এইরূপ।
খরবাণ
।
গোকুলদেব
।
নারায়ণদেব
।
কেশবসেনদেব
।
ঈশানদেব
কেশবদেব একজন বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন এবং তুলাপুরুষ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঈশানদেব অন্তত ১৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাম্রশাসন দুইটির অক্ষরদৃষ্টে অনুমান হয় যে উক্ত রাজগণ ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। দেব উপাধি হইতে অনুমিত হয় যে এই রাজগণও দেববংশীয় ছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের সহিত পূর্ব্বোক্ত দেববংশীয় রাজগণের কোনো সম্বন্ধ ছিল কি না তাহা বলা যায় না। শ্রীহট্টের উকিল শ্ৰীযুক্ত কমলাকান্ত গুপ্ত চৌধুরীর নিকট “হট্টনাথের পাঁচালী” নামক একখানি পুঁথি আছে। ইহাতে এই রাজবংশের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়।
যে স্থানে তাম্রশাসন দুইটি পাওয়া গিয়াছে সেখানে একটি জনপ্রবাদ প্রচলিত আছে যে তথাকার রাজা গৌরগোবিন্দ শাহজালাল কর্ত্তৃক পরাজিত হন। এই ঘটনার তারিখ ১২৫৭ অব্দ। কেশবদেবের এক উপাধি ছিল রিপুরাজ গোপী গোবিন্দ। কেহ কেহ মনে করেন যে এই রাজাই জনপ্রবাদের গৌরগোবিন্দ।
.
২. পট্টিকেরা রাজ্য
বর্ত্তমান কুমিল্লা জিলায় পট্টিকেরা রাজ্য অবস্থিত ছিল। পট্টিকেরা নামে একটি পরগণা এখনো এই প্রাচীন রাজ্যের স্মৃতি বহন করিতেছে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় (১৯৪৩ অব্দ) সামরিক প্রয়োজনে মাটি খনন করার ফলে কুমিল্লার অনতিদূরবর্ত্তী লালমাই বা ময়নামতী পাহাড়ে বহু প্রাচীন স্তূপ, মন্দির প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রায় দশ মাইল ব্যাপিয়া এই সমুদয় প্রাচীন কীৰ্ত্তির চিহ্ন এখনো বিদ্যমান। এই স্থানেই যে প্রাচীন পট্টিকেরা রাজ্যের রাজধানী অথবা অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল তাহা এক প্রকার নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।
১০১৫ অব্দে লিখিত একখানি পুঁথিতে ষোড়শভুজা এক দেবীর চিত্রের নিম্নে লিখিত আছে “পট্টিকেরে চুন্দাবরভবনে চুন্দা”। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে রাজধানী পট্টিকেরে প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ চুন্দা দেবীর মূর্ত্তি একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত ধ্বংসাবশেষ হইতে অনুমিত হয় যে ইহারও ৩-৪ শত বৎসর পূর্ব্বে পট্টিকেরা একটি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল।
ব্রহ্মদেশের ঐতিহাসিক আখ্যানে পট্টিকেরা রাজ্যের বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রহ্মের প্রসিদ্ধ রাজা অনিরুদ্ধ (১০৪৪-১০৭৭ অব্দ) পট্টিকেরা পর্য্যন্ত স্বীয় রাজ্য বিস্তার করেন এবং এই সময় হইতেই দুই রাজ্যের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ব্রহ্মরাজ কনজিথের (১০৮৪-১১১২) কন্যার সহিত পট্টিকেরার রাজপুত্রের ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী ব্রহ্মদেশের আখ্যানে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে এবং এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া তথায় অনেক কবিতা ও নাটক রচিত হইয়াছে। এই সমুদয় নাটক এখনো ব্রহ্মদেশে অভিনীত হয়। ব্রহ্মরাজের ইচ্ছা থাকিলেও রাজনৈতিক কারণে তাঁহার কন্যার সহিত পট্টিকেরার রাজকুমারের বিবাহ অসম্ভব হইলে উক্ত রাজকুমার আত্মহত্যা করেন। কিন্তু এই রাজকন্যার গর্ভজাত পুত্র অলংসিথু মাতামহের মৃত্যুর পর ব্রহ্মদেশের রাজা হন এবং পট্টিকেরার রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন। অলংসিথুর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নরথু সিংহাসনে আরোহণ করিয়া স্বহস্তে তাঁহার বিমাতা পট্টিকেরার রাজকন্যাকে বধ করেন। কন্যার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া পট্টিকেরার রাজা প্রতিশোধ লইতে সংকল্প করিলেন। তিনি আটজন বিশ্বস্ত সৈনিককে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ব্রহ্মদেশের রাজধানী পাগানে পাঠাইলেন। ব্রাহ্মণেরা আশীর্বাদ করিবার ছলে রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া রাজাকে বধ করে এবং সকলেই স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন দেয়। এই সমুদয় কাহিনী কত দূর সত্য বলা যায় না, কিন্তু ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে পট্টিকেরা একটি প্রসিদ্ধ রাজ্য ছিল এবং নিকটবর্ত্তী ব্রহ্মদেশের সহিত তাঁহার রাজনৈতিক সম্বন্ধ ছিল।
ময়নামতী পাহাড়ে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসনে রণবঙ্কমল্ল শ্রীহরিকালদেব নামক পট্টিকেরার এক রাজার নাম পাওয়া যায়। ইনি ১২০৮ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অন্তত ১৭ বৎসর রাজত্ব করেন। এই তাম্রশাসন দ্বারা রাজমন্ত্রী শ্রী ধড়ি-এব পট্টিকেরা নগরে এক বৌদ্ধবিহারে কিঞ্চিৎ ভূমি দান করেন। রাজমন্ত্রীর পিতার নামে হেদি-এব এবং তাম্রশাসনের লেখকের নাম মেদিনী-এব। এই সমুদয় নাম ব্রহ্মদেশীয় নামের অনুরূপ এবং পট্টিকেরা রাজ্যের সহিত ব্রহ্মদেশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের পরিচায়ক।
শ্রীহরিকালদেব প্রাচীন পট্টিকেরা-রাজবংশীয় ছিলেন অথবা নিজেই একটি স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। এই সময়ে যে দেববংশীয় রাজগণ এই অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অসম্ভব নহে যে শ্রীহরিকালদেবও দেববংশীয় ছিলেন। কিন্তু তাঁহার নামের অন্ত স্থিত ‘দেব’ শব্দ বংশপদবী অথবা রাজকীয় সম্মানসূচক পদমাত্র তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। তবে রণবঙ্কমল্ল উপাধিধারী শ্রীহরিকালদেবের পর যে পট্টিকেরা রাজ্য দেববংশীয় দামোদরদেবের রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল ইহাই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়।
১৫. রাজ্যশাসনপদ্ধতি
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ –রাজ্যশাসনপদ্ধতি
১. প্রাচীন যুগ
গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্ব্বে বাংলার রাজ্যশাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে কোনো সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীন গ্রন্থে সুহ্ম পু প্রভৃতি জাতি এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উল্লেখ দেখিয়া অনুমান হয় যে আর্য্যাবর্তের অন্যান্য অংশের ন্যায় বাংলা দেশেও প্রথমে কয়েকটি বিশিষ্ট সংঘবদ্ধ জাতি বসবাস করে এবং ইহা হইতেই ক্রমে রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।
গ্রীক লেখকগণ গঙ্গরিডই রাজ্যের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে কোনো সন্দেহ থাকে না যে খৃষ্টপূৰ্ব চতুর্থ শতাব্দের পূর্ব্বেই বাংলায় রাজতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। কারণ রাজ্যশাসনপদ্ধতি সুনিয়ন্ত্রিত ও বিশেষ শৃঙ্খলার সহিত বিধিবদ্ধ না হইলে এরূপ পরাক্রান্ত রাজ্যের উদ্ভব সম্ভবপর নহে। মহাভারতের উল্লিখিত হইয়াছে যে বাংলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি মিলিত হইয়া বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল এবং তাহারা বিদেশী রাজ্যের সহিতও রাজনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিল। ইহাও বাংলা দেশে রাজনৈতিক জ্ঞানের প্রসার ও প্রভাব সূচিত করে। রাজকুমার বিজয়ের আখ্যান (পৃ. ১৪) সত্য হইলে বাংলা দেশে যে প্রজাশক্তি প্রভাবশালী ছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে।
মৌৰ্য্যযুগের একখানিমাত্র লিপি মহাস্থানগড়ে অর্থাৎ প্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধনে পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে একজন মহামাত্রের উল্লেখ আছে। এই লিপির প্রকৃত মৰ্ম্ম কী তাহা লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। দুর্ভিক্ষ বা অন্য কোনো কারণবশত প্রজাগণের দুরাবস্থা হওয়ায় সরকারী ভাণ্ডার (কোষাগার) হইতে দুস্থ লোকদিগকে শস্য ও নগদ টাকা ধার দিয়া সাহায্য করার আদেশই এই লিপিতে উক্ত হইয়াছে। খুব সম্ভবত মৌর্যগণের সুপরিচিত রাজ্যশাসনপদ্ধতি বাংলা দেশেও প্রচলিত ছিল।
.
২. গুপ্তসাম্রাজ্য ও অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগ
বাংলা দেশ গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত হইলেও ইহার এক অংশমাত্র গুপ্ত সম্রাটগণের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ছিল। শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য এই অংশে বর্ত্তমান কালের ন্যায় কতকগুলি নির্দিষ্ট শাসন বিভাগ ছিল। সৰ্ব্বাপেক্ষা বড় বিভাগের নাম ছিল ভুক্তি। প্রত্যেক ভুক্তি কতকগুলি বিষয়, মণ্ডল, বীথি ও গ্রামে বিভক্ত ছিল। বঙ্গ বিভাগের পূর্ব্বে বাংলার যে অংশকে আমরা রাজসাহী বিভাগ বলিতাম মোটামুটি তাহাই ছিল পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির সীমা। প্রাচীন ভুক্তি ও বর্ত্তমান বর্দ্ধমান বিভাগও মোটামুটি একই বলা যাইতে পারে। বিষয়গুলি ছিল বর্ত্তমান জিলার মতো।
গুপ্ত সম্রাট স্বয়ং ভুক্তির শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিতেন-ইহার উপাধি ছিল উপরিক মহারাজ। সাধারণত উপরিক-মহারাজই অধীনস্থ বিষয়গুলির শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিতেন, কিন্তু কোনো কোনো স্থলে স্বয়ং সম্রাট কর্ত্তৃক তাঁহাদের নির্বাচনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের নানা উপাধি ছিল,–কুমারামাত্য, আযুক্তক, বিষয়পতি প্রভৃতি। ইহা ভিন্ন আরও বহুসংখ্যক কাজকর্ম্মচারীর নাম পাওয়া যায়।
ভুক্তি, বিষয়, বীথি প্রভৃতি প্রত্যেক বিভাগেরই একটি কেন্দ্র ছিল এবং সেখানে তাহাদের একটি অধিকরণ (আফিস) থাকিত। তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ কতকগুলি ভূমি বিক্রয়ের দলিল হইতে এই সমুদয় অধিকরণের কিছু কিছু বিবরণ জানিতে পাওয়া যায়। ইহার কয়েকখানিতে কোটিবর্ষ বিষয়ের অধিকরণের উল্লেখ আছে। কোটিবর্ষ নগরীর ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমানকালে বাণগড় নামে পরিচিত। এই নগরীর নাম অনুসারেই উক্ত বিষয়ের নামকরণ হইয়াছিল এবং এখানেই এই বিষয়ের অধিকরণ অবস্থিত ছিল। বিষয়পতি ব্যতীত এই অধিকরণের আর চারিজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। তাঁহারা নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম সার্থবাহ, প্রথম কুলিক ও প্রথম কায়স্থ। এই চারিটি পদবীর প্রকৃত অর্থ নিরূপণ করা দুরূহ। সম্ভবত প্রথম তিনটি ধনী মহাজন, বণিক ও শিল্পীগণের প্রতিনিধিস্বরূপ অধিকরণের সদস্য ছিলেন। কায়স্থ শব্দে লেখক ও এক শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারী বুঝাইত। সেকালে ধনী মহাজন, বণিক ও শিল্পীগণের বিধিবদ্ধ সংঘ-প্রতিষ্ঠান ছিল। এই সমুদয় সংঘ-মুখ্যগণই সম্ভবত বিষয় অধিকরণের সদস্য হইতেন। ইহা হইতে সেকালের স্বায়ত্তশাসন প্রথার মূল কত দৃঢ় ছিল তাহা বুঝা যায়। প্রতি বিষয়পতি এই সমুদয় বিভিন্ন সংঘের প্রতিনিধির মিলিত হইয়া বিষয়ের কাৰ্য্য নিৰ্ব্বাহ করিতেন। কী প্রণালীতে এই সমুদয় অধিকরণ জমি বিক্রয় করিত তাঁহার বিবরণ পূৰ্ব্বোক্ত তাম্রশাসনগুলি হইতে জানা যায়। প্রথমে ক্রেতা অধিকরণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কী উদ্দেশ্যে কোনো জমি কিনিতে চান তাহা নিবেদন করিতেন। তখন অধিকরণের আদেশে পুস্তপাল নামক একজন কর্ম্মচারী ঐ জমি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া উহা বিক্রয় করা যাইতে পারে কি না এবং উহার মূল্য কত প্রভৃতি বিষয় অধিকরণের গোচর করিতেন। তারপর নির্ধারিত মূল্য দেওয়া হইলে ক্রেতা জমির অধিকার পাইতেন। কোনো কোনো স্থলে দেখা যায় যে এই জমি বিক্রয়ের কথা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামবাসীগণকে জানানো হইত এবং গ্রামের মহত্তর (মাতব্বর) ও কুটুম্বিগণের (গৃহস্থ) সাক্ষাতে জমি মাপিয়া তাঁহার সীমা নির্দিষ্ট করা হইত।
বাংলার যে অংশ প্রত্যক্ষভাবে গুপ্ত সম্রাটগণের শাসনাধীনে ছিল না তাহা সামন্ত মহারাজগণের অধীনে ছিল। সম্ভবত যে সমুদয় স্বাধীন রাজ্য গুপ্তগণের পদানত হইয়াছিল তাহাদের রাজারাই গুপ্তগণের অধীনস্থ সামন্তরাজরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের বিভিন্ন উপাধি দেখিয়া অনুমিত হয় যে ইহারা দেশের আভ্যন্তরিক শাসন বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা পরিচালিত করিতেন। ক্রমে গুপ্তগণের প্রবর্তিত শাসনপদ্ধতি বাংলা দেশের সর্বত্র প্রচলিত হইয়াছিল। দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পরও ভুক্তি, বিষয়, বীথি প্রভৃতি শাসন বিভাগের ও বিষয় অধিকারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য স্বাধীন রাজগণ মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিতেন। গুপ্ত সম্রাটগণের ন্যায় ইঁহারাও বিভিন্ন শ্ৰেণীর বহুসংখক রাজকর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতেন। গোপচন্দ্রের মল্লসারূল তাম্রশাসনে এই কর্ম্মচারীগণের একটি তালিকা পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহাদের কাহার কী কাৰ্য্য বা কী পরিমাণ ক্ষমতা ও দায়িত্ব ছিল অধিকাংশস্থলেই তাহা নির্ণয় করা যায় না।
.
৩. পালসাম্রাজ্য
পালবংশীয় রাজগণের চারি শতাব্দীব্যাপী রাজত্বকালে বাংলায় শাসনপ্রণালী দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। গুপ্তযুগের ন্যায় ভুক্তি, বিষয়, মণ্ডল প্রভৃতি সুনির্দিষ্ট শাসন বিভাগের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। পুণ্ড্রবর্দ্ধন ও বর্দ্ধমান ভুক্তি ব্যতীত বাংলায় আর একটি ভুক্তির প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ইহার নাম দণ্ডভুক্তি। ইহা বর্ত্তমান মেদিনীপুর জিলায় অবস্থিত ছিল। এতদ্ব্যতীত উত্তর বিহারে তীর-ভুক্তি (ত্রিহুত), দক্ষিণ বিহারে শ্রীনগর-ভুক্তি এবং আসামে প্রাগজ্যোতিষ-ভুক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু এই সমুদয় ভুক্তি বা ইহাদের অধীনস্থিত বিষয়, মণ্ডল প্রভৃতির শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না।
পরাক্রান্ত পাল সম্রাটগণ প্রাচীন বাংলার মহারাজ বা পরবর্ত্তীকালের ‘মহারাজাধিরাজ’ পদবীতে সন্তুষ্ট থাকেন নাই। গুপ্ত সম্রাটগণের ন্যায় তাঁহারাও পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ প্রভৃতি গৌরবময় উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজ্য বহু বিস্তৃত হওয়ায় শাসনপ্রণালীরও তদনুরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। এই সময় হইতেই রাজত্বের সমুদয় ব্যাপারে প্রভূত ক্ষমতাসম্পন্ন একজন প্রধানমন্ত্রীর উল্লেখ দেখিতে পাই। গর্গ নামে এক ব্রাহ্মণ ধৰ্ম্মপালের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন–তারপর তাঁহার বংশধরগণই নারায়ণপালের রাজ্য পৰ্য্যন্ত প্রায় একশত বৎসর যাবৎ এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই বংশীয় গুরবমিশ্রের একখানি শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে যে ম্রাট দেবপাল স্বয়ং তাঁহার মন্ত্রী দর্ভপাণির অবসরের অপেক্ষায় তাঁহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন, এবং এই দর্ভপাণি ও তাঁহার পৌত্র কেদারমিশ্রর নীতিকৌশলে ও বুদ্ধিবলেই বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সমুদয় উক্তি অতিরঞ্জিত হইলেও পালরাজ্যে প্রধানমন্ত্রীগণ যে অসাধারণ প্রভুত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী যুগে এইরূপ আর এক মন্ত্রীবংশের পরিচয় পাই। এই বংশীয় যোগদেব তৃতীয় বিগ্রহপালের এবং বৈদ্যদেব কুমারপালের মন্ত্রী ছিলেন। বৈদ্যদেব পরে কামরূপে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।
গুপ্তযুগের ন্যায় পালরাজ্যের অধীনেও অনেক সামন্ত রাজা ছিলেন। ইহাদের মধ্যে রাজা, রাজন্যক, রাজনক, রাণক, সামন্ত ও মহাসামন্ত প্রভৃতি বহু শ্রেণীবিভাগ ছিল। কেন্দ্রীয় রাজশক্তি দুর্বল হইলে এই সমুদয় সামন্তরাজগণ যে স্বাধীন রাজার ন্যায় ব্যবহার করিতেন রামপালের প্রসঙ্গে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।
প্রাচীন ভারতে রাজগণ রাজ্যের শাসন সংরক্ষণ ব্যতীত সমাজ ও অর্থনীতি, এমনকি ধর্ম্মের ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করিতেন। ধর্ম্মপাল শাস্ত্রানুসারে বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্ম প্রতিপালন করিতেন। তিনি নিজে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও হিন্দু প্রজাগণকে তাঁহাদের ধর্ম্মব্যবস্থা অনুসারেই শাসন করিতেন। পালরাজগণের প্রধানমন্ত্রীগণও যে ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন ইহাও সে যুগের ধর্ম্মমত বিষয়ে উদারতা প্রমাণিত করে।
পালরাজগণের তাম্রশাসনে রাজকর্ম্মচারীগণের যে সুদীর্ঘ তালিকা আছে তাহা হইতে বেশ বোঝা যায় যে, রাজ্যশাসনপ্রণালী বিধিবদ্ধ ও সুনিয়ন্ত্রিত ছিল। দুঃখের বিষয় এই সমুদয় রাজকর্ম্মচারীগণের অনেকের সম্বন্ধেই আমাদের কিছু জানা নাই। তাহাদের নাম বা উপাধি হইতে যেটুকু অনুমান করা যায় তাহা ব্যতীত শাসনপ্রণালী ও বিভিন্ন কর্ম্মচারীর কর্তব্য ও ক্ষমতা সম্বন্ধে আর কিছুই জানিবার উপায় নাই। এই কর্ম্মচারীর তালিকা বিশ্লেষণ করিয়া যে সামান্য তথ্য পাওয়া যায় এখানে মাত্র তাঁহারই উল্লেখ করিতেছি।
কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত শাসনপ্রণালীতে দেখিতে পাই যে রাজ্যের সমুদয় শাসনকাৰ্য্য নিৰ্ব্বাহের জন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট শাসন বিভাগ ছিল এবং ইহার প্রত্যেকটির জন্য একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইতেন। পালরাজগণও মোটামুটি এই ব্যবস্থার অনুসরণ করিতেন। কয়েকটি প্রধান প্রধান শাসন বিভাগ ও তাঁহার কর্ম্মচারীগণের সম্বন্ধে যাহা জানা যায় তাহা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইল।
১। কেন্দ্রীয় শাসন-প্রধানমন্ত্রী এবং আরও অনেক মন্ত্রী ও অমাত্যের সাহায্যে রাজা স্বয়ং এই বিভাগ পরিচালনা করিতেন। এই সমুদয়ের মধ্যে ‘মহাসান্ধিবিগ্ৰহিক’ একজন প্রধান অমাত্য ছিলেন। অপর রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করাই ছিল তাঁহার কাজ। দূতও একজন প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন এবং বিদেশীয় রাজ্যের সহিত প্রত্যক্ষভাবে যোগসূত্র রক্ষা করিতেন। ‘রাজস্থানীয়’ ও ‘অঙ্গরক্ত’ নামে দুইজন অমাত্যের উল্লেখ আছে। ইহারা সম্ভবত যথাক্রমে রাজার প্রতিনিধি ও দেহরক্ষীর দলের নায়ক ছিলেন। অনেক সময়, বিশেষত রাজা বৃদ্ধ হইলে, যুবরাজ শাসন বিষয়ে পিতাকে সাহায্য করিতেন। পালরাজগণের লিপিতে ও রামচরিতে যুবরাজগণের উল্লেখ আছে।
২। রাজস্ব বিভাগ-বিভিন্ন প্রকার রাজস্ব আদায়ের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারী নির্দিষ্ট ছিল। উৎপন্ন শস্যের উপর নানাবিধ কর ধার্য্য হইত, যথা, ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য, উপরিকর প্রভৃতি,-এবং সম্ভবত গ্রামপতি ও বিষয়পতিরাই ইহা সংগ্রহ করিতেন। ‘ষষ্ঠাধিকৃত’ নামে একজন কর্ম্মচারীর উল্লেখ আছে। মনুস্মৃতি অনুসারে কতকগুলি দ্রব্যের ষষ্ঠভাগ রাজার প্রাপ্য ছিল,-সম্ভবত উক্ত কর্ম্মচারী এই কর আদায় করিতেন। ‘চৌরোদ্ধরণিক’, ‘শৌল্কিক’, ‘দাশাপরাধিক’ ও ‘তরক’ নামক কর্ম্মচারীরা সম্ভবত যথাক্রমে, দস্যু ও তস্করের ভয় হইতে রক্ষার জন্য দেয় কর, বাণিজ্যদ্রব্যের শুল্ক, চৌৰ্যাদি অপরাধের নিমিত্ত অর্থদণ্ড এবং খেয়াঘাটেরও মাশুল আদায় করিতেন।
৩। ‘মহাক্ষপটলিক’ ও ‘জ্যেষ্ঠকায়স্থ’ সম্ভবত হিসাব ও দলিল বিভাগ পর্যবেক্ষণ করিতেন।
৪। ‘ক্ষেত্রপ’ ও ‘প্রমাতৃ’ সম্ভবত জমির জরিপ বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন।
৫। ‘মহাদণ্ডনায়ক’ অথবা ‘ধর্ম্মাধিকার’ বিচার বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন।
৬। মহাপ্রতীহার’, ‘দাণ্ডিক’, ‘দাপাশিক’ ও ‘দণ্ডশক্তি সম্ভবত পুলিশ বিভাগের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন।
৭। সৈনিক বিভাগ-এই বিভাগে অধ্যক্ষের উপাধি ছিল সেনাপতি অথবা মহাসেনাপতি। পদাতিক, অশ্বারোহী, হস্তী, উষ্ট্র ও রণতরী সৈন্যদলের এই কয়টি প্রধান বিভাগ ছিল। ইহার প্রত্যেকের জন্য একজন স্বতন্ত্র অধ্যক্ষ ছিল। এতদ্ব্যতীত ‘কোট্টপাল’ (দুর্গরক্ষক), ‘প্রান্তপাল’ (রাজ্যের সীমান্তরক্ষক) প্রভৃতি নামও পাওয়া যায়।
বাংলা দেশে, বিশেষত দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গে, রণতরী যুদ্ধসজ্জার একটি প্রধান উপকরণ ছিল। বহু প্রাচীনকাল হইতেই বাংলার নৌবাহিনী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল! কালিদাস রঘুবংশে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলার প্রাচীন লিপিতেও তরীর উল্লেখ আছে। কুমারপাল ও বিজয়সেনের রাজত্বে যে নৌযুদ্ধ হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। বাংলার সামরিক হস্তীর প্রসিদ্ধিও প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত। ভারতের পূৰ্ব্বপ্রান্তে বহু হস্তী পাওয়া যাইত এবং এখনো যায়। কিন্তু বাংলায় উৎকৃষ্ট অশ্বের অভাব ছিল। পালরাজগণ সুদূর কামোজ হইতে যুদ্ধের অশ্ব সংগ্রহ করিতেন। ভারতের এই প্রদেশ চিরকালই অশ্বের জন্য প্রসিদ্ধ। পালরাজগণের একখানিমাত্র তাম্রশাসনে রথের উল্লেখ আছে। কিন্তু এই যুগের যুদ্ধে রথের খুব ব্যবহার হইত না।
পালরাজগণের তাম্রশাসনে অমাত্যগণের তালিকার শেষে “গৌড়-মালব-খশ-হূণ-কুলিক-কর্ণাট-লাট” প্রভৃতি জাতির উল্লেখ আছে। খুব সম্ভবত ভারতের এই সমুদয় জাতি হইতে পালরাজগণ সৈন্য সংগ্রহ করিতেন এবং বর্ত্তমানকালের মারহাট্টা, বেলুচি, গুর্খা রেজিমেন্টের ন্যায় ঐ সমুদয় ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় সৈন্য দ্বারা সৈন্যদল গঠিত হইত।
.
৪. সেনরাজ্য ও অন্যান্য খরাজ্য
পালরাজ্যের যে শাসনপদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছিল তাহা মোটামুটিভাবে সেন, কাম্বোজ, চন্দ্র বর্ম্মবংশীয় রাজগণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য কোনো কোনো বিষয়ে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল।
ভুক্তি, মণ্ডল ও বিষয় ব্যতীত পাঠক, চতুর, আবৃত্তি প্রভৃতি কয়েকটি নূতন শাসনকেন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেনরাজ্য পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির সীমা অনেক। বাড়িয়েছিল। বঙ্গ-বিভাগের পূর্ব্ববর্ত্তী রাজসাহী, ঢাকা ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ এবং সম্ভবত বর্ত্তমানকালের চট্টগ্রাম বিভাগেরও কতক অংশ এই ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। অর্থাৎ ইহা উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে সমুদ্র এবং পশ্চিমে ভাগীরথী হইতে মেঘনা অথবা তাঁহার পূৰ্ব্বভাগের প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। অপর দিকে বর্দ্ধমান ভুক্তির সীমা কমাইয়া ইহার উত্তর অংশে কঙ্কগ্রাম নামে নূতন একটি ভুক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।
সেনবংশীয় লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার পুত্রগণ পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ ব্যতীত ‘অশ্বপতি, গজপতি, নরপতি, রাজত্রয়াধিপতি’ প্রভৃতি নূতন পদবীও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনুকরণে দেববংশীয় দশরথদেবও এই সমুদয় উপাধি ব্যবহার করিতেন।
পালরাজগণের ন্যায় সেনরাজগণের তাম্রশাসনেও সামন্ত, অমাত্য প্রভৃতির সুদীর্ঘ তালিকা পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার মধ্যে কিছু কিছু নূতনত্ব আছে। সেনরাজগণের তালিকায় রাণীর নাম আছে কিন্তু পালরাজগণের একখানি তাম্রশাসনেও এই সুদীর্ঘ তালিকায় রাণীর নাম পাওয়া যায় না। চন্দ্র, বৰ্ম ও কামোজ রাজগণের তাম্ৰশাসনোক্ত তালিকায়ও রাণীর নাম পাওয়া যায়। এই যুগে রাজ্যশাসন বিষয়ে রাণীর কোনো বিশেষ ক্ষমতা ছিল, অথবা বাংলার বাহির হইতে আগত এই সমুদয় রাজবংশের আদিম বাসস্থানে রাণীর বিশেষ কোনো অধিকার ছিল বলিয়া তাঁহারা বাংলায় এই নূতন প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা বলা কঠিন। কাম্বোজ, বৰ্ম্ম ও সেনরাজবংশের তাম্রশাসনে পুরোহিতের নাম পাওয়া যায়। সেনরাজগণের শেষযুগে পুরোহিতের স্থানে মহাপুরোহিতের উল্লেখ আছে। ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মাবলম্বী এই তিন রাজবংশের রাজ্যকালে হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের সহিত রাজশক্তির সম্বন্ধ যে পূৰ্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল ইহা তাহাই সূচিত করে।
‘মহামুদ্ৰাধিকৃত’ ও ‘মহাসর্ব্বাধিকৃত’ নামে দুইজন নূতন উচ্চপদস্থ অমাত্যের নাম পাওয়া যায়। এই শেষোক্ত নাম হইতেই বাংলার ‘সর্ব্বাধিকারী’ পদবীর উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এইরূপ বিচার বিভাগে মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ, রাজস্ব বিভাগে ‘হট্টপতি’ এবং সৈন্য বিভাগে ‘মহাপীলুপতি’, ‘মহাগণস্থ’ এবং ‘মহাব্যুহপতি’ প্রভৃতি আরও কয়েকটি নূতন নাম পাই।
কামোজরাজ নয়পালের তাম্রশাসনে যেভাবে অমাত্যগণের উল্লেখ আছে তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই তালিকায় আছে “করণসহ অধ্যক্ষবর্গ; সৈনিক-সঙ্ মুখ্যসহ সেনাপতি; গূঢ়পুরুষসহ দূত; এবং মন্ত্রপাল”। “করণসহ অধ্যক্ষবর্গ” এই সমষ্টিসূচক শব্দ হইতে প্রমাণিত হয় যে একজন অধ্যক্ষ কয়েকজন করণ অর্থাৎ কেরাণীর সহযোগে একটি শাসন বিভাগ তদন্ত করিতেন, এবং নির্দিষ্টসংখ্যক এইরূপ কতকগুলি অধ্যক্ষের দ্বারা দেশের সমুদয় আভ্যন্তরিক শাসনের কাৰ্যনিৰ্বাহ হইত। সৈন্য বিভাগেও বিভিন্ন শ্রেণীর সৈন্যদলের সঙ্ ছিল এবং তাহাদের অধিনায়কদের সহযোগে সেনাপতি এই বিভাগের কাৰ্য্য নিৰ্বাহ করিতেন। পররাষ্ট্র বিভাগ স্বতন্ত্র ছিল এবং ‘দূত’, ‘গূঢ়পুরুষ’ (গুপ্তচর) গণের সহায়তায় ইহার কাৰ্য্য নিৰ্বাহ করিতেন। সর্বোপরি ছিলেন মন্ত্রপাল’ অর্থাৎ মন্ত্রীগণ। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে যে শাসনপদ্ধতির বর্ণনা আছে ইহার সহিত তাঁহার খুবই সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। চন্দ্র, বৰ্ম ও সেনরাজগণের তাম্রশাসনে অমাত্যের যে সুদীর্ঘ তালিকা আছে। তাঁহার যে “এবং অধ্যক্ষ-প্রচারোক্ত অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ” এই উক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অর্থশাস্ত্রের যে অধ্যায়ে শাসনপদ্ধতির বিবরণ আছে তাঁহার নাম ‘অধ্যক্ষপ্রচার’। এই সমুদয় কারণে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের যে শাসনপদ্ধতি বর্ণিত আছে তাঁহার অনুকরণেই বাংলার শাসনপদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছিল।
বাংলার শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে যাহা বলা হইল তাহা অতিশয় সামান্য এবং ইহা হইতে এ সম্বন্ধে স্পষ্ট বা সঠিক কোনো ধারণা করা কঠিন। কিন্তু আপাতত ইহার বেশী জানিবার উপায় নাই। তবে যেটুকু জানা গিয়াছে তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে বাংলায় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দী বা তাঁহার পূৰ্ব্ব হইতেই ধীরে ধীরে একটি বিধিবদ্ধ শাসনপ্রণালী গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং পাল ও সেনযুগে তাহা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা ভারতের অন্যান্য প্রদেশের শাসনপদ্ধতির অনুরূপ ছিল বলিয়াই মনে হয়। অন্তত বাংলা দেশ যে এই বিষয়ে কম অগ্রসর হইয়াছিল এরূপ মনে করিবার কোনো সঙ্গত কারণ নাই।
১৬. ভাষা ও সাহিত্য
১৬. ষোড়শ পরিচ্ছেদ –ভাষা ও সাহিত্য
১. বাংলা ভাষার উৎপত্তি
সৰ্ব্বপ্রাচীন যুগে আর্য্যগণ যে ভাষা ব্যবহার করিতেন, এবং যে ভাষায় বৈদিক গ্রন্থাদি লিখিত হইয়াছিল, কালপ্রভাবে তাঁহার অনেক পরিবর্ত্তন হয়, এবং এই পরিবর্ত্তনের ফলেই ভারতবর্ষে প্রাচীন ও বর্ত্তমানকালে প্রচলিত বহু ভাষার উদ্ভব হইয়াছে। এই ভাষা-বিবর্ত্তনের সুদীর্ঘ ইতিহাস বর্ণনা করা এই গ্রন্থে সম্ভবপর নহে। তবে নিম্নলিখিত তিনটি শ্রেণীবিভাগ হইতে এ সম্বন্ধে কতক ধারণা করা যাইবে।
১। প্রাচীন সংস্কৃত ঋগ্বেদের সময় হইতে ৬০০ খৃ. পূ. পৰ্য্যন্ত
২। পালি-প্রাকৃত-অপভ্রংশ–৬০০ খৃ. পূ.-১০০০ খৃষ্টাব্দ।
৩। অপভ্রংশ হইতে বাংলা ও অন্যান্য দেশীয় ভাষার উৎপত্তি-১০০০ খৃষ্টাব্দ হইতে
আৰ্য্যগণ বাংলায় আসিবার পূর্ব্বে বাংলার অধিবাসীগণ যে ভাষার ব্যবহার করিতেন তাঁহার কোনো নিদর্শন বর্ত্তমান নাই। তবে ইহার কোনো কোনো শব্দ বা রচনাপদ্ধতি যে সংস্কৃত ও বর্ত্তমান বাংলায় আত্মগোপন করিয়া আছে তাহা খুবই সম্ভব, এবং ইহার কিছু কিছু চিহ্নও পণ্ডিতগণ আবিষ্কার করিয়াছেন। ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়া ইহার মূল্য খুব বেশী হইলেও বর্ত্তমান প্রসঙ্গে এই আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। যত দূর প্রমাণ পাওয়া যায় তাহাতে অনুমিত হয় যে আর্য্যগণের সংস্পর্শে ও প্রভাবে বাংলার প্রাচীন অধিবাসীগণ নিজেদের ভাষা ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে আৰ্যভাষা গ্রহণ করেন। উপরে যে শ্ৰেণীভাগ করা হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, যে যুগে আর্য্যগণ এদেশে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন তখন প্রাচীন সংস্কৃত হইতে প্রথমে পালি এবং প্রাকৃত ও পরে অপভ্রংশ, এই তিন ভাষার উৎপত্তি হয়। বাংলা দেশেও এই সমুদয় ভাষা প্রচলিত ছিল, কিন্তু ইহাতে কোনো সাহিত্য রচিত হইয়া থাকিলেও তাঁহার বিশেষ কোনো নিদর্শন বর্ত্তমান নাই। অপভ্রংশ হইতে বাংলা প্রভৃতি দেশীয় ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। বাংলার যে সৰ্ব্বপ্রাচীন দেশী ভাষার নমুনা পাওয়া গিয়াছে তাহা দশম শতাব্দীর পূর্ব্বেকার বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন না। এই ভাষা হইতেই কালে বর্ত্তমান বাংলা ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু সে হিন্দু যুগের পরের কথা। এই দেশীয় ভাষায় রচিত যে কয়েকটি পদ পাওয়া গিয়াছে তাঁহার সংখ্যা বেশী নহে। কিন্তু ইহা ছাড়া হিন্দযুগে বাঙ্গালীর সাহিত্য প্রধানত সংস্কৃত ভাষায়ই রচিত হইয়াছিল। সুতরাং প্রথমে বাংলার সংস্কৃত সাহিত্যেরই আলোচনা করিব।
.
২. পালযুগের পূৰ্ব্বেকার সংস্কৃত সাহিত্য
মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত বাংলার সৰ্ব্বপ্রাচীন প্রস্তরলিপি প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। ইহাই বাংলায় মৌর্যযুগের একমাত্র সাহিত্যিক নিদর্শন। ইহার পাঁচশত বৎসরেরও অধিক পরে সুসুনিয়া পৰ্ব্বতগাত্রে উত্তীর্ণ রাজা চন্দ্রবর্ম্মার লিপি ও গুপ্তযুগের তাম্রশাসনগুলি, সংস্কৃত ভাষায় রচিত। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে, এবং সম্ভবত তাঁহার বহু পূর্ব্বেই, এদেশে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট চর্চ্চা ছিল, কিন্তু এই যুগের অন্য কোনো রচনা এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। বাংলা দেশে যে উচ্চশিক্ষা ও বিদ্যাচর্চ্চার বিশেষ প্রসার ছিল, চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান (৫ম শতাব্দী), হুয়েন সাং ও ই-সিং (৭ম শতাব্দী) তাঁহার বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন।
এই চর্চ্চার ফলে সপ্তম শতাব্দীতে বাংলার সংস্কৃত সাহিত্য একটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছিল। বাণভট্টের একটি প্রসিদ্ধ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের যে সমুদয় আদর্শ গুণ তাঁহার সবগুলি একত্রে কোনো দেশেই প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু এক এক দেশের সাহিত্যে এক একটি গুণ প্রকটিত হয়; যেমন উত্তর দেশীয় সাহিত্যে ‘শ্লেষ’, পাশ্চাত্যে ‘অর্থ’, দক্ষিণে ‘উৎপ্রেক্ষা’ এবং গৌড়দেশে ‘অক্ষর-ডম্বর’। কেহ কেহ এই শ্লোক হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গৌড়দেশের রাজা শশাঙ্কের ন্যায় গৌড়দেশীয় সাহিত্যকেও বাণভট্ট বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতেন এবং এই শ্লোকে তাঁহার নিন্দাই করিয়াছেন। কিন্তু এই অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। শব্দ-বিন্যাস সাহিত্যের অন্যতম গুণ, এবং গৌড়ীয় সাহিত্যে যে শ্লেষ, অর্থ ও উৎপ্রেক্ষা অপেক্ষা এই গুণেরই প্রাচুর্য দেখিতে পাওয়া যায় ইহা ব্যক্ত করাই সম্ভবত বাণভট্টের অভিপ্রায় ছিল। ভামহ ও দণ্ডী (৭ম ও ৮ম শতাব্দী) যেভাবে গৌড় মার্গ ও গৌড়ী রীতির উল্লেখ করিয়াছেন তাহাও উপরোক্ত অনুমানের সমর্থন করে। তাঁহাদের মতে তখন সংস্কৃত কাব্যে গৌড়ী ও বৈদভী এই দুইটিই প্রধান রীতি ছিল। ভামহের মতে গৌড়ী এবং দণ্ডীর মতে বৈদভী ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।
মোটের উপর এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বেই বাঙ্গালীর প্রতিভা সংস্কৃত সাহিত্যে একটি অভিনব রচনারীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছিল। এই রচনারীতির কিছু কিছু নিদর্শন ত্রিপুরায় প্রাপ্ত লোকনাথের তাম্রশাসন ও নিধানপুরে প্রাপ্ত ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে পাওয়া যায়। প্রথমটি পদ্যে ও দ্বিতীয়টি গদ্যে লিখিত। এ যুগে যে বাংলায় অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই–কিন্তু তাঁহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে। যাহা আছে তাহাও এদেশীয় বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করার কোনো উপায় নাই।
এই যুগের কতকগুলি গ্রন্থ বাঙ্গালীর রচিত বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ একখানি। চারি খণ্ডে ও ১৬০ অধ্যায়ে বিভক্ত এই বিশাল গ্রন্থে হস্তীর নানারূপ ব্যাধির আলোচনা করা হইয়াছে। ঋষি পালকাপ্য চম্পা নগরীতে অঙ্গদেশের রাজা রামপাদের নিকট ইহা বিবৃত করেন এবং ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে তাঁহার আশ্রম ছিল-উক্ত গ্রন্থে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, এই গ্রন্থ বাংলা দেশে লিখিত হইয়াছিল, কিন্তু ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ একমত নহেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ইহার তারিখ খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার সমর্থক কোনো প্রমাণ নাই। অমরকোষ ও অগ্নিপুরাণে এই গ্রন্থের উল্লেখ আছে এবং কালিদাসের রঘুবংশে সম্ভবত ইহার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ইহা সত্য হইলে হস্তায়ুর্ব্বেদ গ্রন্থ অন্তত কালিদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। গ্রন্থ প্রণেতা ঋষি পালকাপ্য সম্ভবত কাল্পনিক নাম। এক হস্তিনীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল এরূপ কথিত হইয়াছে।
চান্দ্র ব্যাকরণ একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহার প্রণেতা চন্দ্রগোমিন্ সম্ভবত বাঙ্গালী ছিলেন। ইনি পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন, এবং পাণিনির সূত্রগুলি নূতন প্রণালীতে বিভক্ত করিয়া যে ব্যাকরণ গ্রন্থ ও তাঁহার বৃত্তি রচনা করেন তাহা সমগ্র ভারতবর্ষে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। কাশ্মীর, নেপাল, তিব্বত ও সিংহল দ্বীপে ইহার পঠনপাঠন বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। চন্দ্রগোমিন্ বৌদ্ধ ছিলেন। তিব্বতীয় কিংবদন্তী অনুসারে ‘ন্যায়সিদ্ধালোক’ নামক দার্শনিক গ্রন্থ এবং ৩৬ খানি তন্ত্রশাস্ত্রের রচয়িতা চন্দ্রগোমিন্ ও উল্লিখিত বৈয়াকরণিক চন্দ্রগোমি একই ব্যক্তি; তিনি বরেন্দ্রভূমিতে এক ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তথা হইতে নির্বাসিত হইয়া চন্দ্রদ্বীপে বাস করেন এবং পরে নালন্দায় স্থিরমতির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইহার সম্বন্ধে তিব্বতে যে সমুদয় আখ্যান প্রচলিত আছে একবিংশ পরিচ্ছেদে তাহা বিবৃত হইবে। চন্দ্রগোমিন্ উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ব্যতীত তারা ও মঞ্জুশ্রীর স্তোত্র, ‘লোকানন্দ’ নাটক ও ‘শিষ্য-লেখ-ধৰ্ম্ম’ নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। লোকানন্দ নাটকের তিব্বতীয় অনুবাদ মাত্র পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু শিষ্য-লেখ-ধর্ম্মের মূল ও অনুবাদ উভয়ই বর্ত্তমান।
প্রসিদ্ধ দার্শনিক গৌড়পাদ সম্ভবত বাঙ্গালী ছিলেন-কারণ তিনি গৌড়াচাৰ্য্য নামে অভিহিত হইয়াছেন। প্রচলিত প্রবাদ অনুসারে ইনি শঙ্করাচার্য্যের পরমগুরু অর্থাৎ গুরুর গুরু ছিলেন। ইহার রচিত আগম-শাস্ত্র ‘গৌড়পাদকারিকা’ নামে পরিচিত। ইহার দার্শনিক তথ্য শঙ্করের পূর্ব্বে প্রচলিত বেদান্ত মতবাদ ও মাধ্যমিক শূন্যবাদের সমন্বয়; ইহার কোনো কোনো অংশে বৌদ্ধ প্রভাব লক্ষিত হয়। গৌড়পাদ এতদ্ব্যতীত ঈশ্বরকৃষ্ণ রচিত সাংখ্যকারিকার টীকা করেন; মাঠরবৃত্তির সহিত ইহার অনেক সাদৃশ্য আছে।
চন্দ্রগোমিন্ ও গৌড়পাদ ব্যতীত এই যুগের আর কোনো বাঙ্গালি গ্রন্থকারের নাম এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। কিন্তু এ যুগে যে বাংলায় বহু সংস্কৃত কবি ও পণ্ডিত জন্মিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের গ্রন্থ ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল বাণভট্ট, ভামহ ও দণ্ডী এবং চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণের লেখা হইতে তাহা আমরা নিঃসন্দেহে জানিতে পারি।
.
৩. পালযুগে সংস্কৃত সাহিত্য
পালরাজগণের বহুসংখ্যক তাম্রশাসনে যে সমুদয় সংস্কৃত শ্লোক আছে তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে এই যুগে বাংলায় সংস্কৃত কাব্য চর্চ্চা ও কাব্য রচনা আরও প্রসার লাভ করিয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও যে এই যুগে বাঙ্গালীরা পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন এই সমুদয় তাম্রশাসনে তাঁহারও প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। নারায়ণপালের মন্ত্রী গুরবমিশ্র তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের প্রশস্তিতে লিখিয়াছেন যে দেবপালের মন্ত্রী দৰ্ভপাণি চতুর্বেদে ব্যুৎপন্ন ছিলেন ও কেদারমিশ্র চতুর্বিদ্যাপয়োধি পান করিয়াছিলেন। তিনি নিজে বেদ, আগম, নীতি ও জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শিতা ও বেদের ব্যাখ্যা দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এইরূপে পালযুগের অন্যান্য তাম্রশাসনে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বৈদিক সাহিত্য, মীমাংসা, ব্যাকরণ, তর্ক, বেদান্ত ও প্রমাণশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। চতুর্ভুজ তাঁহার হরিচরিত কাব্যে লিখিয়াছেন যে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ব্যাকরণ ও কাব্যে বিচক্ষণ ছিলেন। হরিবৰ্ম্মদেবের মন্ত্রী ভট্টভবদেবের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। প্রশস্তিকার লিখিয়াছেন যে, তিনি দর্শন, মীমাংসা, অর্থশাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র, আয়ুর্ব্বেদ, অস্ত্রবেদ, সিদ্ধান্ত, তন্ত্র এবং গণিতে পারদর্শী ছিলেন এবং হোরাশাস্ত্রে গ্রন্থ লিখিয়া ‘দ্বিতীয় বরাহ’ উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিভিন্ন তাম্রশাসনে ভূমিদান-গ্রহণকারী ব্রাহ্মণগণের যে পরিচয় আছে তাহা হইতে তাঁহাদের বেদের বিভিন্ন শাখায় পাণ্ডিত্য ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপে প্রচুর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।
সুতরাং বাংলায় যে সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা বহুল পরিমাণে ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় বৌদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থ ব্যতীত এই যুগে বাঙ্গালীর রচিত গ্রন্থ যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা এইরূপ বহু শতাব্দীব্যাপী বিস্তৃত চর্চ্চার নিদর্শন হিসেবে নিতান্তই সামান্য ও অকিঞ্চিৎকর।
মুদ্রারাক্ষস প্রণেতা নাট্যকার বিশাখদত্ত, অনর্ঘরাঘবের কবি মুরারি, চণ্ডকৌশিক নাটকের গ্রন্থকার ক্ষেমীশ্বর, কীচকবধ কাব্য প্রণেতা নীতিবর্ম্মা এবং নৈষধ-চরিত রচয়িতা শ্রীহর্ষ-এই সকল প্রসিদ্ধ লেখক বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়া কেহ কেহ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে ইহাদের কাহাকেও বাঙ্গালার সন্তান বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায় না।
অভিনন্দ নামে একজন বাঙ্গালী কবির সন্ধান পাওয়া যায়। শার্গধর-পদ্ধতিতে ইঁহাকে গৌড় অভিনন্দ বলা হইয়াছে, সুতরাং ইনি যে বাঙ্গালী ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অভিনন্দের রচনা বলিয়া যে সমুদয় শ্লোক বিভিন্ন প্রসিদ্ধ পদ্যসংগ্রহ গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে, সম্ভবত সে সমুদয় তাঁহারই রচনা। কেহ কেহ মনে করেন যে ইনিই কাদম্বরী-কথা-সার নামক কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা। অভিনন্দ সম্ভবত নবম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।
পালযুগের একখানি কাব্যগ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা সন্ধ্যাকরনন্দী প্রণীত ‘রামচরিত’ কাব্য। ইহার রচনাপ্রণালী, ঐতিহাসিক মূল্য ও আখ্যানভাগ রামপালের ইতিহাস প্রসঙ্গে সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। এই দুরূহ শ্লেষাত্মক কাব্যের প্রতি শ্লোক এমন সুকৌশলে রচিত হইয়াছে যে পৃথক পৃথকভাবে বর্ণবিন্যাস ও শব্দযোজনা করিলে ইহা একদিকে রামায়ণের রামচন্দ্রের ও অপরদিকে পালসম্রাট রামপালের পক্ষে প্রযোজ্য হইবে। এই গ্রন্থের উপসংহারে একটি কবিপ্রশস্তি আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে সন্ধ্যাকরনন্দী বরেন্দ্রে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের নিকট বাস করিতেন। তাঁহার পিতা প্রজাপতিনন্দী রামপালের সান্ধি বিগ্রহিক ছিলেন। মদনপালের রাজত্বকালে এই কাব্য রচিত হয়। দ্ব্যর্থবোধক শ্লোকের দ্বারা ঐতিহাসিক আখ্যান বর্ণনা হেতু এই কাব্যে কবিত্বশক্তি সর্বত্র পরিস্ফুট হইবার সুযোগ পায় নাই। কিন্তু বরেন্দ্র ও রামাবতী নগরীর বর্ণনা ও ভীমের সহিত যুদ্ধের বিবরণ প্রভৃতি সাহিত্যের দিক দিয়াও উপভোগ্য। উচ্চাঙ্গের কবিত্ব না থাকিলেও ‘রামচরিত’ বাঙ্গালীর সংস্কৃত কাব্যে নিষ্ঠা ও নৈপুণ্যের পরিচয় হিসেবে চিরদিনই সমাদৃত হইবে।
দর্শনশাস্ত্রে আমরা এই যুগের মাত্র একজন প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী লেখকের নাম জানি। ইনি বিখ্যাত ন্যায়কন্দলী প্রণেতা শ্রীধরভট্ট। ইঁহার পিতার নাম বলদেব, মাতার নাম অব্বোকা, এবং জন্মভূমি দক্ষিণ রাঢ়ের অন্তর্গত ভূরিশ্রেষ্ঠি (বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী ভুরশুট গ্রাম)। প্রশস্তপাদ বৈশেষিক সূত্রের যে ‘পদার্থ-ধৰ্ম্ম’ সংগ্রহ নামক ভাষ্য রচনা করেন শ্রীধরভট্ট তাঁহার ন্যায়কন্দলী টীকা দ্বারা ন্যায়বৈশেষিক মতের উপর আস্তিক্যবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। শ্রীধর ‘অদ্বয় সিদ্ধি’, ‘তত্ত্বসংবাদিনী’, ‘তপ্রবোধ’ এবং সগ্রহটীকা প্রভৃতি বেদান্ত ও মীমাংসাবিষয়ক কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন-কিন্তু ইহার একখানিও পাওয়া যায় নাই। ন্যায়কন্দলীর রচনাকাল ৯১৩ (অথবা ৯১০) শকাব্দ (৯৯১ অথবা ৯৮৮ অব্দ)।
জিনেন্দ্রবুদ্ধি, মৈত্রেয়রক্ষিত এবং বিমলমতি প্রভৃতি এই যুগের কয়েকজন বিখ্যাত বৈয়াকরণিক এবং অমরকোষের টীকাকার সুভূতিচন্দ্রকে কেহ কেহ বাঙ্গালী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু ইহার সমর্থক সন্তোষজনক প্রমাণ এখনো কিছু পাওয়া যায় নাই।
বৈদ্যক শাস্ত্রে কয়েকজন বাঙ্গালী গ্রন্থকার প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। সুবিখ্যাত ‘রুগবিনিশ্চয়’ অথবা ‘নিদান’ গ্রন্থের প্রণেতা মাধব বাঙ্গালী ছিলেন কি না সন্দেহের বিষয়। কিন্তু চরক ও সুশ্রুতের প্রসিদ্ধ টীকাকার চক্রপাণিদত্ত যে বাঙ্গালী ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাঁহার ‘চিকিৎসা সংগ্রহ’ গ্রন্থে তিনি নিজের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে তিনি লোধুবংশীয় কুলীন ছিলেন; তাঁহার পিতা নারায়ণ গৌড়াধিপের পাত্র ও রসবত্যধিকারী (অর্থাৎ রন্ধনশালার অধ্যক্ষ) [কেহ কেহ এই পদের পাঠান্তর কল্পনা করিয়া লিখিয়াছেন যে চক্রপাণিদত্ত নিজেই গৌড়াধিপের পাত্র ছিলেন], এবং তাঁহার ভ্রাতা একজন বিচক্ষণ চিকিৎসক ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে শিবদাসসেন এই গ্রন্থের টীকায় লিখিয়াছেন যে উক্ত গৌড়াধিপ নয়পাল। ইহা সত্য হইলে চক্রপাণিদত্ত একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অথবা প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। তিনি চিকিত্সা সংগ্রহ এবং ‘আয়ুর্ব্বেদ দীপিকা’ নামক চরকের ও ‘ভানুমতী’ নামক সুশ্রুতের টীকা ব্যতীত ‘শব্দচন্দ্রিকা’ ও ‘দ্রব্যগুণ সংগ্রহ’ নামক আরও দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। নিশ্চলকর ‘রত্নপ্রভা’ নামে ‘চিকিৎসা সংগ্রহের’ যে টীকা লিখিয়াছেন তাহাতে বহু বৈদ্যক গ্রন্থের উল্লেখ আছে। নিশ্চলকর খুব সম্ভবত বাঙ্গালী ছিলেন এবং তিনি সম্রাট রামপাল ও কামরূপ রাজার সাক্ষাতের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে তিনি রামপালের সমসাময়িক ছিলেন।
সুরেশ্বর অথবা সুরপাল নামে আর একজন বাঙ্গালী বৈদ্যক গ্রন্থকার দ্বাদশ শতাব্দে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহার পিতামহ দেবগণ রাজা গোবিন্দচন্দ্রের এবং পিতা ভদ্রেশ্বর রামপালের সভায় রাজবৈদ্য ছিলেন। তিনি নিজে রাজা ভীমপালের বৈদ্য ছিলেন। সুরেশ্বর আয়ুৰ্ব্বেদোক্ত উদ্ভিদের পরিচয় দিবার জন্য শব্দ-প্রদীপ ও ‘বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ’ নামে দুইখানি এবং ঔষধে লৌহের ব্যবহার সম্বন্ধে ‘লোহ-পদ্ধতি বা ‘লোহ-সর্ব্বস্ব’ নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।
পালযুগে, বিশেষত দশম ও একাদশ শতাব্দীতে, বাংলায় বৈদ্যক শাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। অনেকে মনে করেন যে বৈদ্যক গ্রন্থের টীকাকার অরুণদত্ত, বিজয় রক্ষিত, বৃন্দ কুণ্ড, শ্রীকণ্ঠ দত্ত, বঙ্গসেন এবং সুশ্রুতের প্রসিদ্ধ টীকাকার গয়দাস বাঙ্গালী ছিলেন এবং ইহাদের অনেকেই পালযুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।
‘চিকিৎসা-সার সংগ্রহের’ গ্রন্থকার বঙ্গসেন সম্ভবত বাঙালী ছিলেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না।
বাংলায় যে বৈদিক সাহিত্যের চর্চ্চা হইত তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। দশম শতাব্দীতে ‘কুসুমাঞ্জলি’ প্রণেতা উদয়ন (কেহ কেহ ঘঁহাকে বাঙ্গালী বলেন) লিখিয়াছেন যে বাংলার মীমাংসকগণ বেদের প্রকৃত মৰ্ম্ম জানেন না। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও এইরূপ বলিয়াছেন। মীমাংসাশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তির অভাব সূচিত করিলেও ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে বাংলায় এই বিষয়ে চর্চ্চা ও গ্রন্থ রচিত হইত। অনিরুদ্ধভট্ট ও ভবদেবভট্ট উভয়েই কুমারিলের গ্রন্থে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। কিন্তু ভবদেব প্রণীত ‘তৌতাতিত-মত-তিলক’ ব্যতীত বাঙ্গালী রচিত আর কোনো মীমাংসা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় নাই। বৈদিক কৰ্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে উত্তর রাঢ় নিবাসী নারায়ণ ‘ছান্দোগ্য পরিশিষ্টে’র ‘প্রকাশ’ নামক টীকা রচনা করিয়াছিলেন। নারায়ণ দেবপালের সমসাময়িক ছিলেন। ভবদেবভট্টও ‘ছান্দোগ্য কৰ্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি’ লিখিয়াছিলেন। ইহা ‘দর্শকর্ম্মপদ্ধতি’, ‘দশকৰ্ম্মদীপিকা’ ও ‘সংস্কারপদ্ধতি’ নামেও পরিচিত।
ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক বাঙ্গালী গ্রন্থ লিখিয়াছেন। জিতেন্দ্রিয়, বালক এবং যোগ্লোক নামে তিনজন লেখকের বচন ও মত পরবর্ত্তী লেখকগণ বহুস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন-কিন্তু ইহাদের মূল গ্রন্থগুলি পাওয়া যায় নাই। ভবদেবভট্ট প্রণীত ‘প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ’ এ বিষয়ে একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহা সম্পূর্ণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার ব্যবহার তিলক গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই। আচার সম্বন্ধে তাঁহার গ্রন্থও পাওয়া যায় নাই। ভবদেবভট্টের এই সমুদয় গ্রন্থ ভারতের প্রসিদ্ধ স্মার্তগণ শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন।
জীমূতবাহন সম্ভবত ভবদেবভট্টের পরবর্ত্তী, কিন্তু তাঁহার সঠিক কাল নির্ণয় সম্ভব নহে। জীমূতবাহন রাঢ়দেশীয় পারিভদ্ৰকুলে জন্মগ্রহণ করেন। এই পারিভদ্ৰকুল রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের ‘পারিহাল’ বা ‘পারি’ গাঁঈর অন্তর্গত। জীমূতবাহন প্রণীত ‘দায়ভাগ’ অনুসারে এখন পর্য্যন্তও বাংলার উত্তরাধিকার, স্ত্রীধন প্রভৃতি বিধিগুলি পরিচালিত হইতেছে। বাংলার বাহিরে ভারতের সৰ্ব্বত্র মিতাক্ষরা আইন প্রচলিত। সুতরাং জীমূতবাহনের মত বাঙ্গালীর একটি বৈশিষ্ট্য সূচিত করিতেছে। তৎপ্রণীত ‘ব্যবহার-মাতৃকা’ বিচারপদ্ধতি সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। ইহাও বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাঁহার তৃতীয় গ্রন্থ ‘কাল বিবেক। হিন্দুগণের আচরিত বিবিধ অনুষ্ঠানের কাল নিরূপণ করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। সৌভাগ্যের বিষয় জীমূতবাহনের তিনখানি গ্রন্থই অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে এবং বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে।
পালরাজগণ বৌদ্ধ ছিলেন এবং এই সময় ভারতবর্ষে একমাত্র তাহাদের রাজ্যেই অর্থাৎ বাংলায় ও বিহারেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি বেশ দৃঢ় ছিল। এই যুগে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃতিও অনেক পরিবর্তিত হইয়াছিল এবং মহাযানের পরিবর্তে সহজযান বা সহজিয়া ধৰ্ম্ম প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। সপ্তদশ পরিচ্ছেদে এই বিষয় বিস্তারিত উল্লিখিত হইবে। সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের এক বিপুল সাহিত্য আছে। তাঁহার অধিকাংশই বাঙ্গালীর রচিত। তাহারা যে সমুদয় গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন তাঁহার অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তিব্বতীয় ভাষায় এই সমুদয় গ্রন্থের যে অনুবাদ হইয়াছিল তাহা অবলম্বন করিয়া আমরা এই বিরাট ধর্ম্মসাহিত্যের স্বরূপ নির্ণয় করিতে পারি। যে সমুদয় গ্রন্থের প্রণেতা বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়া তিব্বতীয় সাহিত্যে স্পষ্ট উল্লেখ আছে তাহা ছাড়াও হয়তো আরও অনেক বাঙ্গালী গ্রন্থকার ছিলেন। কিন্তু এ বিষয়ে আর কোনো প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত আমরা তাঁহাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। কিন্তু যেটুকু জানা গিয়াছে তাহা হইতে নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে পালযুগের এই তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাহিত্য বাঙ্গালীর একটি বিশেষ মূল্যবান সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। গ্রন্থকারগণের নাম, পরিচয় ও কাল-নির্ণয় লইয়া অনেক গোলমাল ও বিভিন্ন মতবাদ আছে; এ স্থানে তাঁহার উল্লেখের প্রয়োজন নাই। যে সমুদয় বাঙ্গালীর লেখায় এই তান্ত্রিক সাহিত্য সৃষ্ট ও পুরিপুষ্ট হইয়াছিল মোটামুটিভাবে তাঁহাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ হইল।
পালযুগের পূৰ্ব্ববর্ত্তী হইলেও এই প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম মহাযান লেখক শীলভদ্রের নাম করিতে হয়। তাঁহার মাত্র একখানি গ্রন্থ (‘আৰ্য-বুদ্ধ-ভূমি-ব্যাখ্যান’) তিব্বতীয় অনুবাদে রক্ষিত হইয়াছে।
শান্তিদেব নামে দুইজন তান্ত্রিক সাহিত্যের রচয়িতা ছিলেন। আবার ঠিক এই নামধারী একজন মহাযান গ্রন্থের লেখকও আছেন। এই দুই শান্তিদেব এক কি না এবং তিনি বাঙ্গালী কি না নিশ্চিত বলা যায় না। শান্তি রক্ষিত সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। জেরি নামে দুইজন বাঙ্গালী বৌদ্ধ সাহিত্যিক ছিলেন। প্রাচীন জেরি বরেন্দ্রে রাজা সনাতনের রাজ্যে বাস করিতেন এবং দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের গুরু ছিলেন। তৎপ্রণীত তিনখানি ন্যায়ের গ্রন্থের এবং অপর জেরির রচিত ১১ খানি বজ্রযান সাধন গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদ মাত্র পাওয়া যায়।
দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ ও জগদ্বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি ১৬৮ খানি গ্রন্থের রচয়িতা। এই সমুদয়ের অধিকাংশই বজ্রযান সাধন গ্রন্থ।
জ্ঞানশ্রীমিত্র ‘কাৰ্য-কারণ-ভাব-সিদ্ধি’ নামক ন্যায় গ্রন্থের প্রণেতা। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মাধব তাঁহার ‘সৰ্ব্বদর্শন-সংগ্রহে’ এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার তিব্বতীয় অনুবাদ মাত্র পাওয়া যায়।
অভয়াকর গুপ্ত ২০ খানি বজ্রযান গ্রন্থের লেখক। ইহার মধ্যে মাত্র চারিখানির মূল সংস্কৃত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।
এ পর্য্যন্ত যে সমুদয় গ্রন্থকারের নামোল্লেখ করা হইল ইহারা সকলেই বাংলার বাহিরে বহু খ্যাতি ও কীৰ্ত্তি অর্জন করিয়াছেন এবং ইহাদের সংক্ষিপ্ত জীবনী একবিংশ অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে।
অন্যান্য যে সমুদয় বৌদ্ধ গ্রন্থকার তিব্বতীয় কিংবদন্তী অনুসারে বাঙ্গালী ছিলেন তাঁহাদের নাম, রচিত গ্রন্থ ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে লিপিবদ্ধ হইল :
| নাম | গ্রন্থ (তিব্বতীয় অনুবাদে রক্ষিত) | সংক্ষিপ্ত পরিচয় |
| ১। দিবাকরচন্দ্র | হেরুক সাধন ও ২ খানি অনুবাদ | নয়পালের রাজ্যকালে মৈত্রীপার শিষ্য ছিলেন। |
| ২। কুমারচন্দ্র | ৩ খানি তান্ত্রিক পঞ্জিকা | বিক্রমপুরী বিহারের একজন অবধূত। |
| ৩। কুমারবজ্র | হেরুক সাধক | |
| ৪। দানশীল | ‘পুস্তক পাঠোপায়’ ও ৬০ খানি তান্ত্রিকগ্রন্থের অনুবাদক | জগদ্দল বিহারে ছিলেন। |
| ৫। পুতলি | বোধিচিত্ত-বায়ু চরণ-ভাবনোপায় | বঙ্গাল দেশীয় শূদ্র এবং ৮৪ সিদ্ধের অন্যতম। |
| ৬। নাগবোধি | ১৩ খানি তান্ত্রিক গ্রন্থ | বঙ্গালদেশে শিবসেনা নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। |
| ৭। প্রজ্ঞাবর্ম্মণ | তান্ত্রিকগ্রন্থের ২ খানি টীকা ও অনুবাদ। |
এতদ্ব্যতীত তিব্বতীয় গ্রন্থে বাংলার বিভিন্ন বৌদ্ধবিহারের কয়েকজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের উল্লেখ আছে, কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন কি না তাহা সঠিক জানা যায় না। ইঁহাদের মধ্যে সোমপুর বিহারের বোধিভদ্র এবং জগদ্দল বিহারের মোক্ষাকরগুপ্ত, বিভূতিচন্দ্র এবং শুভাকরের নাম করা যাইতে পারে।
দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বাংলায় বহু বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল; এই সম্বন্ধে সপ্তদশ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে। এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকগণ সিদ্ধাচাৰ্য্য নামে খ্যাত। এই সমুদয় সিদ্ধাচার্যগণ অনেকেই অপভ্রংশ অথবা প্রাচীন বাংলায় তাঁহাদের ধর্ম্মমত প্রচার করিয়াছেন। এই সমুদয় গ্রন্থের তিব্বতীয় অনুবাদ ও কতকগুলির মূল পাওয়া গিয়াছে। এই সিদ্ধাচাৰ্যগণের নাম, তারিখ ও বিবরণ সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে; তাঁহার সবিস্তার উল্লেখ না করিয়া সংক্ষেপে ইহাদের পরিচয় দিতেছি। ইঁহাদের প্রণীত দোহা অর্থাৎ প্রাচীন বাংলায় রচিত পদ পরে আলোচিত হইবে।
কুক্কুরপাদ বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিব্বতীয় প্রবাদ অনুসারে তিনি ডাকিনী দেশ হইতে মন্ত্রযান (হেরুক সাধন) এবং অন্যান্য তন্ত্রমত আনিয়া এদেশে প্রচার করেন। শবরীপাদ বঙ্গালদেশের পাহাড়ে শিকার করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তিনি ও তাঁহার দুই স্ত্রী, লোকী ও গুণী নাগার্জুনের নিকট দীক্ষা লাভ করেন।
সিদ্ধাচাৰ্য্যগণের মধ্যে লুইপাদ (অথবা লুই-পা) সমধিক প্রসিদ্ধ। তিনি সম্ভবত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের সমসাময়িক। তিনি ৪ খানি বজ্রযান গ্রন্থ এবং বহু দোহা রচনা করেন। তিব্বতীয় প্রবাদ অনুসারে তিনি বাংলা দেশে ধীবর বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং যোগিনীতন্ত্রের প্রবর্ত্তন করেন।
অনেকে মনে করেন লুইপাদ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ একই ব্যক্তি। কারণ মৎস্যেন্দ্রনাথ যে নূতন ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তন করেন তাঁহার সহিত যোগিনী তন্ত্রের অনেক সাদৃশ্য আছে এবং তিনিও বাংলা দেশের চন্দ্রদ্বীপে ধীবর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার ধর্ম্মমত সংস্কৃত গ্রন্থ ও দোহায় প্রচারিত হয়। সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে ‘কৌলজ্ঞান-নির্ণয়’ সর্বপ্রাচীন ও সমধিক প্রসিদ্ধ।
মৎস্যেন্দ্রনাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। বাংলার রাজা গোপীচাঁদের সন্ন্যাস অবলম্বনে রচিত বহু গীতিকা সমস্ত আৰ্য্যাবর্তে সুপ্রসিদ্ধ। এই গোপীচাঁদ ও তাঁহার মাতা ‘নাথ’ নামে পরিচিত এবং ইহার আচাৰ্য্যগণ সংস্কৃত, অপভ্রংশ ও প্রাচীন বাংলায় বহু গ্রন্থ ও পদ রচনা করিয়াছেন।
অন্যান্য সিদ্ধাচাৰ্য্যগণের মধ্যে কৃষ্ণপাদ (অথবা কানুপা), সরহপাদ প্রভৃতি নাম করা যাইতে পারে।
.
৪. সেনযুগে সংস্কৃত সাহিত্য
সেনরাজগণের অভ্যুদয়ের ফলে অপভ্রংশ ও বাংলায় রচিত তান্ত্রিক সহজিয়া সাহিত্যের প্রসার কমিয়া পুনরায় সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতির যুগ আরম্ভ হয়। সেনরাজগণ শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম্মের উপাসক ছিলেন এবং বৈদিক যাগযজ্ঞ ও ক্রিয়াকাণ্ডের অনুষ্ঠান করিতেন। সুতরাং তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গদেশেও সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দুধর্ম্মের নবজাগরণের সূত্রপাত হয়।
বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক মতের প্রভাবে হিন্দুর আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াপদ্ধতি অনেকটা লোপ পাইয়াছিল। সুতরাং এই সম্বন্ধীয় গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। বল্লালসেনের গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট হারলতা ও পিতৃদয়িত’ নামক দুইখানি গ্রন্থে অশৌচ, শ্রাদ্ধ, সন্ধ্যা, তর্পণ প্রভৃতি হিন্দুর বিবিধ অনুষ্ঠানের ও নিত্যকর্মের বিস্তৃত আলোচনা করেন। বল্লালসেন নিজে ‘ব্ৰত-সাগর’, ‘আচার-সাগর’, ‘প্রতিষ্ঠা-সাগর’, ‘দানসাগর’, ও ‘অদ্ভুতসাগর’ নামক পাঁচখানি গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু মাত্র শেষোক্ত দুইখানি গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীন বহু ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে মত ও উক্তি উদ্ধৃত করিয়া বল্লালসেন এই সমুদয় গ্রন্থে হিন্দুর নানা আচার, প্রতিষ্ঠান, দান কৰ্ম্মাদি ও শুভাশুভাদি নানা নৈমিত্তিক লক্ষণ প্রভৃতির বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। বল্লালসেনের এই সমুদয় গ্রন্থ যে বাংলায় ও বাংলার বাহিরে প্রামাণিক বলিয়া গণ্য হইত তাঁহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে।
হলায়ূধ এই যুগের একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার। তিনি অল্প বয়সেই রাজপণ্ডিত ছিলেন; লক্ষ্মণসেন তাঁহাকে যৌবনে মহামাত্য এবং প্রৌঢ় বয়সে ধৰ্ম্মাধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। হলায়ূধ ‘ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব’, ‘মীমাংসা-সৰ্ব্বস্ব’, ‘বৈষ্ণব-সর্ব্বস্ব’, ‘শৈব-সর্ব্বস্ব’ ও ‘পণ্ডিত-সর্ব্বস্ব’ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন; কিন্তু ব্রাহ্মণ-সৰ্ব্বস্ব ব্যতীত আর কোনো গ্রন্থ এযাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই। হলায়ূধ লিখিয়াছেন যে রাঢ় ও বরেন্দ্রের ব্রাহ্মণগণ বেদ পড়িতেন না এবং বৈদিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রকৃত জ্ঞান ছিল না-এইজন্য হিন্দুর আহ্নিক অনুষ্ঠান ও বিবিধ সংস্কারে ব্যবহৃত বৈদিক মন্ত্রের তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা করিবার জন্য তিনি ব্রাহ্মণ-সৰ্ব্বস্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থ বঙ্গদেশে ও বাহিরে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। হলায়ুধের দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঈশান ও পশুপতি শ্রাদ্ধ ও অন্যান্য দৈনিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে দুইখানি ‘পদ্ধতি’ রচনা করেন। পশুপাতি শ্রাদ্ধপদ্ধতি ব্যতীত পাক্যজ্ঞ সম্বন্ধেও একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।
ভাষাতত্ত্বেও এই যুগের দুই-একজন গ্রন্থকার প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে আৰ্ত্তিহর-পুত্র বন্দ্যঘটীয় সর্ব্বানন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ‘টীকাসৰ্ব্বস্ব’ নামে হঁহার রচিত অমরকোশের টীকা ভারতের সর্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সর্ব্বানন্দ ১১৫৯-৬০ অব্দে এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি অপূৰ্ব্ব পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন এবং বহু দেশী শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমুদয় দেশী শব্দের অধিকাংশই এখনো বাংলা ভাষায় প্রচলিত।
‘ভাষাবৃত্তি’, ত্রিকাণ্ডশেষ’, ‘হারাবলী’, ‘বর্ণদেশনা’ ও ‘দ্বিরূপকোষ’ প্রভৃতি কোষ ও ব্যাকরণ গ্রন্থের রচয়িতা পুরুষোত্তম বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু এই মতের সমর্থক নিশ্চিত কোনো প্রমাণ নাই।
সেনরাজগণ প্রায় সকলেই কবিতা রচনা করিতেন, এবং এই যুগকে বাংলায় সংস্কৃত কাব্যের সুবর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। লক্ষ্মণসেনের সভাসদ ও সুহৃদ বটুদাসের পুত্র শ্রীধর দাস ১২০৬ অব্দে ‘সদুক্তিকর্ণামৃত’ নামে সংস্কৃত কবিতা সংগ্রহ প্রকাশিত করেন। ইহাতে ৪৮৫ জন কবির রচিত ২৩৭০টি মনোজ্ঞ কবিতা সংগৃহীত হইয়াছে। এই কবিগণের মধ্যে অনেকেই অজ্ঞাত এবং সম্ভবত বঙ্গদেশীয় ছিলেন; কিন্তু ইহা সঠিক জানিবার উপায় নাই। সদুক্তিকর্ণামৃতে রাজা বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেনের এবং কেশবসেনের রচিত কবিতা আছে। লক্ষ্মণসেনের রাজসভায় ধোয়ী, উমাপতিধর, গোবর্দ্ধন, শরণ ও জয়দেব এই পাঁচজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। ইঁহাদের বহু কবিতা শ্রীধরদাসের সংগ্রহে পাওয়া যায়।
কবি ধোয়ী তাঁহার একটি শ্লোকে লক্ষ্মণসেনকে রাজা বিক্রমাদিত্যের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই তুলনা কেবলমাত্র কবিসুলভ অত্যুক্তি নহে। তাঁহার সভার উক্ত পঞ্চ কবি সত্য সত্যই পঞ্চ রত্ন ছিলেন।
কবি ধোয়ীর ‘পবনদূত’ কাব্য মেঘদূতের অনুকরণে রচিত। গৌড়ের রাজা লক্ষ্মণসেন যখন দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হইয়া দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন তখন মলয় পৰ্ব্বতের গন্ধৰ্ব্বকন্যা কুবলয়বতী তাঁহার রূপে মুগ্ধ হন এবং পবনমুখে তাঁহার প্রণয়কাহিনী রাজার নিকট প্রেরণ করেন-এই ভূমিকার উপর ১০৪টি শ্লোকে সম্পূর্ণ এই দূতকাব্য রচিত হইয়াছে। কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণে যে সমুদয় দূতকাব্য রচিত হইয়াছে তাঁহার মধ্যে পবনদূতের স্থান খুব উচ্চ। পবনদূত ব্যতীত ধোয়ী সম্ভবত অন্য কাব্যও লিখিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা পাওয়া যায় না। জয়দেব ধোয়ীকে কবিক্ষ্মাপতি অর্থাৎ কবিগণের রাজা এবং শ্রুতিধর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।
উমাপতিধর সম্বন্ধে জয়দেব লিখিয়াছেন ‘বাচ: পল্লবয়তি’ অর্থাৎ তিনি বাক্যবিন্যাসে পটু। তাঁহার রচিত বিজয়সেনের প্রশস্তি (দেওপাড়া লিপি) এই মন্তব্যের সমর্থন করে। মাধাই নগরে প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনের একটি শ্লোকও সদুক্তিকর্ণামৃতে উমাপতিধরের রচিত বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং এই তাম্রশাসনও সম্ভবত তাঁহারই রচনা। সদুক্তিকর্ণামৃতে উমাপতিধরের ৯০টি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে এবং উমাপতিরচিত ‘চন্দ্রচূড়-চরিত’ কাব্যের উল্লেখ আছে। সম্ভবত এই উমাপতি ও উমাপতিধর একই ব্যক্তি।
আচাৰ্য গোবর্দ্ধন সম্বন্ধে জয়দেব লিখিয়াছেন যে শৃঙ্গার রসাত্মক কবিতা রচনায় তাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না। এই কবি গোবর্দ্ধনই যে ‘আৰ্য্যাসপ্তশতীর’ কবি গোবর্দ্ধনাচাৰ্য সে বিষয়ে বিশেষ কোনো সন্দেহ নাই। এই কাব্যগ্রন্থ গোবর্দ্ধনের অপূৰ্ব্ব কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যশক্তির পরিচায়ক। সম্ভবত তাঁহার পাণ্ডিত্যের জন্যই তিনি আচার্য্য বলিয়া অভিহিত হইতেন।
কবি শরণ সম্বন্ধে জয়দেব লিখিয়াছেন যে তিনি শ্লাঘ্য দুরূহ-দ্রুতে অর্থাৎ দুরূহ রচনায় তিনি দ্রুত সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ইহা হইতে কেহ কেহ মনে করেন যে তিনি ও দুর্ঘটবৃত্তির’ গ্রন্থকার বৈয়াকরণিক শরণ একই ব্যক্তি। কিন্তু ইহা অনুমান মাত্র। সদুক্তিকর্ণামৃতে শরণের কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার কোনো কাব্যগ্রন্থ পাওয়া যায় নাই।
লক্ষ্মণসেনের সভাকবিদের মধ্যে জয়দেব যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। তাঁহার গীতগোবিন্দের ‘কোমল-কান্ত-পদাবলী’ কেবলমাত্র বৈষ্ণবগণের নহে, সাহিত্যরস-পিপাসু মাত্রেরই চিত্তে চিরদিন আনন্দদান করিবে। সংস্কৃত ভাষায় এরূপ শ্রুতিমধুর, জনপ্রিয়, অথচ উচ্চাঙ্গের রসসম্পন্ন কাব্য খুব বেশি নাই। ইহার ৪০ খানি বা ততোধিক টীকা আছে এবং ইহার অনুকরণে প্রায় ১২।১৪ খানি কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সমগ্র ভারতে গীতগোবিন্দ যে কিরূপ সমাদর লাভ করিয়াছে ইহাই তাঁহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই অসাধারণ জনপ্রিয়তার জন্যই কবি জয়দেবকে মিথিলা ও উড়িষ্যার অধিবাসীরা তাঁহাদের স্বদেশবাসী বলিয়া দাবি করিয়া থাকেন। কিন্তু অজয় নদের তীরে কেন্দুবিল্বগ্রাম তাঁহার জন্মভূমি, এই প্রবাদ এত দৃঢ়ভাবে প্রচলিত যে বিশেষ প্রমাণ না পাইলে অন্যরূপ বিশ্বাস করা কঠিন। এখনো প্রতি বৎসর মাঘী সংক্রান্তিতে জয়দেবের স্মৃতি রক্ষার্থে কেন্দুবিন্ত্রে বিরাট মেলার অধিবেশন হয়। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। গীতগোবিন্দের একটি শ্লোক হইতে জানা যায় যে তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব এবং মাতার নাম রামদেবী (পাঠান্তর-রাধাদেবী, বামাদেবী)। তাঁহার স্ত্রীর নাম সম্ভব পদ্মাবতী। জয়দেব যে সঙ্গীতে নিপুণ ছিলেন তাঁহার গীতগোবিন্দ রচনা হইতে তাহা বুঝা যায়। কারণ ইহার অনেক পদ প্রকৃতপক্ষে সঙ্গীতের উপযোগী করিয়াই রচিত এবং এখনো গীত হয়।
গীতগোবিন্দে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, এবং বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায় রসশাস্ত্রের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হিসেবে ইহাকে তাহাদের একখানি বিশিষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া গণ্য করেন। কিন্তু ইহার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ছাড়িয়া দিলেও কেবলমাত্র ভাব ও রসের বিচারে ইহা সংস্কৃত সাহিত্যে একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য। ইহা প্রচলিত সংস্কৃত কাব্য হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রকৃতির এবং সাহিত্যিক জগতে এক নতুন সৃষ্টি। রচনাপ্রণালীর দিক হইতে সংস্কৃত কাব্য অপেক্ষা অপভ্রংশ এবং বাংলা ও মৈথিলী ভাষায় রচিত পদাবলীর সহিত ইহার সাদৃশ্য অনেক বেশী। কেহ কেহ মনে করেন যে গীতগোবিন্দ প্রথমে অপভ্রংশ অথবা প্রাচীন বাংলায় রচিত হইয়াছিল এবং পরে সংস্কৃতে রূপান্তরিত হয়। কিন্তু অনেকেই এই মত গ্রহণ করেন নাই।
দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ বাংলায় সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ যুগ বলা যাইতে পারে। একদিকে ধর্ম্মশাস্ত্র ও অপরদিকে উচ্চাঙ্গের কাব্য এই যুগকে অমর করিয়া রাখিয়াছে। অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে অনিরুদ্ধ ভট্ট, হলায়ূধ, বল্লালসেন, সর্ব্বানন্দ, জয়দেব, উমাপতি, ধোয়ী, গোবর্দ্ধন ও শরণ-এতগুলি পণ্ডিত ও কবির সমাবেশ যেকোনো দেশের পক্ষেই গৌরবজনক।
.
৫. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য
স্বাভাবিক বিবর্ত্তনের ফলে সংস্কৃত ভাষা হইতে ক্রমে ক্রমে পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ ও দেশীয় ভাষার উৎপত্তির কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কোন সময়ে বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয় তাহা নিশ্চিত বলা যায় না। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপালে কতকগুলি প্রাচীন বৌদ্ধ-চর্য্যাপদ আবিষ্কার করেন এবং বৌদ্ধগান ও দোহা’ নামক গ্রন্থে প্রকাশিত করেন। বর্ত্তমান বাংলা ভাষার সহিত অনেক প্রভেদ থাকিলেও এই চর্য্যাপদগুলিই যে সর্বপ্রাচীন বাংলা ভাষার নিদর্শন তাহা সকলেই স্বীকার করেন।
এই চর্য্যাপদগুলির প্রত্যেকটিতে চারি হইতে ছয়টি পদ আছে। এগুলির বিষয়বস্তু সহজিয়া বৌদ্ধমতের গূঢ় আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। এ পর্য্যন্ত মোট ২২ জন কবি রচিত ৪৭টি চর্য্যাপদ পাওয়া গিয়াছে। এই পদগুলির সংস্কৃত টীকা আছে-কিন্তু তাহাও এত দুরূহ যে সকল স্থলে মূলের তাৎপর্য বোধগম্য হয় না। এই প্রাচীন বাংলায় রচিত চর্যাপদের সঙ্গে শৌরসেনী অপভ্রংশ ভাষায় রচিত সরহ ও কাহ্নের দোহা এবং ‘ডাকার্ণব’ এই তিনখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে দশম শতাব্দে এইগুলি রচিত হয়। ঐযুগে বাংলায় ও বাংলার বাহিরে শৌরসেনী অপভ্রংশই বহুল পরিমাণে সাহিত্যের ভাষা ছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বাংলাও ক্রমশ পরিপুষ্ট হইয়া সাহিত্যের উপযুক্ত ভাষা বলিয়া পরিগণিত হয়, এবং একই কবি শৌরসেনী অপভ্রংশ ও বাংলা এই দুই ভাষাতেই কবিতা রচনা করেন। খুব সম্ভব এই প্রাচীন বাংলা আরও দুই-একশত বৎসর পূর্ব্ব হইতেই অর্থাৎ পালযুগের প্রারম্ভেই প্রচলিত ছিল, কিন্তু যে চর্য্যাপদগুলি ইহার সৰ্ব্বপ্রাচীন নিদর্শন তাহা সম্ভবত দশম শতাব্দীতে রচিত। তখনো শৌরসেনী অপভ্রংশই আর্য্যাবর্তের পূর্ব্বভাগে সাধুভাষা বলিয়া সম্মানের আসন পাইত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া বাংলার একমাত্র সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত হয়। মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে নবম হইতে দ্বাদশ এই চারি শতাব্দীই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আদিম যুগ।
পূৰ্ব্বে যে ৮৪ জন সিদ্ধাচার্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহারাই পূর্ব্বোক্ত দোহা ও চর্য্যাপদগুলির রচয়িতা। এগুলি তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। তেঙ্গুর নামক বিখ্যাত তিব্বতীয় গ্রন্থে ৫০টি চর্যাপদের অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ৪৭টি ব্যতীত আরও তিনটি প্রাচীন বাংলা চর্য্যাপদ ছিল,-শাস্ত্রী মহাশয়ের আবিষ্কৃত পুঁথি খণ্ডিত হওয়ায় এই তিনটির মূল পাওয়া যায় নাই।
বাংলায় প্রচলিত ময়নামতীর গানে চর্য্যাপদ রচয়িতা এই সিদ্ধাচার্যগণের কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। ময়নামতী রাজা গোপীচাঁদের মাতা ও গোরক্ষনাথের শিষ্যা ছিলেন। তিনি যোগবলে জানিতে পারিলেন যে তাঁহার পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন। গোপীচাঁদ তাঁহার দুই রাণী অদুনা ও পদুনার বহু বাধা সত্ত্বেও মাতার আজ্ঞায় সন্ন্যাসী হইলেন এবং গোরক্ষনাথের শিষ্য জালন্ধরিপাদ অথবা হাড়িপার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।
সিদ্ধ ও যোগীপুরুষ হিসাবে গোরক্ষনাথের খ্যাতি ভারতের সর্বত্র বিস্তৃত, এবং তপ্রবর্তিত কানফাটা যোগী সম্প্রদায় সমগ্র হিন্দুস্থানে, বিশেষত পাঞ্জাবে ও রাজপুতনায়, এখন পর্য্যন্ত বিশেষ প্রভাবশালী। তাঁহার পুত্র মীননাথ অথবা মৎস্যেন্দ্রনাথ। স্বয়ং শিব তাঁহাকে গুহ্য মন্ত্র প্রদান করেন এবং তিনি আদি সিদ্ধ নামে কথিত হইয়া থাকেন। ময়নামতীর গানে এই সম্প্রদায়ের নিম্নলিখিত রূপ গুরুপরম্পরা পাওয়া যায়।
মৎস্যোন্দ্রনাথ (মনীনাথ)
।
গোরক্ষনাথ (গোরখনাথ)
।
জালন্ধরিপাদ (হাড়িপা)
।
কৃষ্ণপাদ (কানুপা, কাহ্নপা)
যে ৪৭টি চর্য্যাপদ পাওয়া গিয়াছে তাঁহার মধ্যে ১২টির রচয়িতা কৃষ্ণপাদ বা কাহ্নপা। তিনি একটি পদে যেভাবে জালন্ধরিপাদের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় যে ইনি তাঁহার গুরু। সুতরাং পদরচয়িতা কৃষ্ণপাদ ও গোরক্ষনাথের প্রশিষ্য কৃষ্ণপাদ একই ব্যক্তি এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। লুইপা দুইটি চৰ্য্যাপদের রচয়িতা। তিব্বতীয় আখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া কেহ ঘঁহাকে আদি সিদ্ধ মৎস্যেন্দ্রনাথের সহিত অভিন্ন মনে করেন, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই সমুদয় পদরচয়িতা সিদ্ধ গুরুদিগের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা একমত নহেন। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেন যে গোরক্ষনাথ দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু ড. শহীদুল্লাহ নেপালের প্রচলিত কিংবদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে মৎস্যেন্দ্রনাথ সপ্তম শতাব্দের লোক। কিন্তু অনেকেই এই মত গ্রহণ করেন না। চর্যাপদের ভাষা দশম শতাব্দীর পূৰ্ব্বকার নহে, ইহাই প্রচলিত মত।
চর্য্যাপদগুলিকে বাংলা সাহিত্যের আদিম উৎস বলা যাইতে পারে এবং ইহার প্রভাবেই পরবর্ত্তী যুগের বাংলার সহজিয়া গান, বৈষ্ণব পদাবলী, শাক্ত ও বাউল গান প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের দিক দিয়া ইহার মূল্য খুব বেশী। নিছক সাহিত্য হিসাবে সৌন্দৰ্য্য বিকাশিত হইবার সুযোগ পায় নাই-কিন্তু মাঝে মাঝে ইহাতে প্রকৃত কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। নিম্নে নমুনাস্বরূপ একটি প্রাচীন চর্য্যাপদ ও বর্ত্তমান বাংলা ভাষায় তাঁহার যথাসম্ভব রূপান্তর দেখানো হইতেছে। ইহা হইতে প্রাচীন চর্যাপদের ভাষা ও ভাব সম্বন্ধে ধারণা অনেকটা স্পষ্ট হইবে।
চর্য্যাপদ ১৪
১। গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বইই নাঈ।
তহিঁ চড়িলী মাতঙ্গি পোইআ লীলে পার করেই।
২। বাহ তু ডোম্বী বাহ লো ডোম্বী বাটত ভইল উছারা।
সদ্গুরু পাআ-পসাএঁ জাইব পুণু জিমউরা৷
৩। পাঞ্চ কেড়ুআল পড়ন্তেঁ মাঙ্গে পীঠত কাছী বান্ধী।
গঅন উখোলেঁ সিঞ্চহু পাণী ন পইসই সান্ধি৷
৪। চান্দ সুজ দুই চাকা সিঠি সংহার পুলিন্দা।
বাম দাহিণ দুই মাগ ন চেবই বাহ তু ছন্দা।।
৫। কবড়ী ন লেই বোড়ী ন লেই সুচ্ছলে পার করেই।
জো রথে চড়িলা বাহবা ‘। জানি কুলেঁ কুল বুলই।।
বর্ত্তমান বাংলায় রূপান্তর
১। গঙ্গা যমুনা মধ্যে যে বহে নৌকা।
তাহাতে চড়িয়া চণ্ডালী ডোবা লোককে অবলীলাক্রমে পার করে।
২। বাহ্ ডোমনী! বাহ্ লো ডোমনী! পথে হইল বেলা গত।
সদ্গুরু-পাদ-প্রসাদে যাইব পুনঃ জিনপুর (জিন= বুদ্ধ) ॥
৩। পাঁচ দাঁড় পড়িতে নৌকার গলুইয়ে, পিঠে কাছি বান্ধিয়া।
গগন-উখলিতে (দ্বারা) ছেঁচ পানি, না পসিবে সন্ধিতে। (ছিদ্রে জল প্রবেশ করিবে না)।।
৪। চাঁদ-সূৰ্য্য দুই চাকা, সৃষ্টি-সংহার (দুই) মাস্তুল।
বাম ডাহিনে দুই মার্গ না বোধ হয়, বাহ্ স্বচ্ছন্দে।।
৫। কড়ি না লয়, বুড়ি (পয়সা) না লয়, অমনি পার করে।
যে রথে চড়িল, (নৌকা) বাহিতে না জানিয়া কূলে কূলে বেড়ায়।।
চর্য্যাপদ ব্যতীত যে ঐযুগে প্রাচীন বাংলায় রচিত অন্যান্য শ্রেণীর সাহিত্য ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে কিছু কিছু প্রমাণও আছে। চালুক্যরাজ তৃতীয় সোমেশ্বরের রাজ্যকাল (১১২৭-১১৩৮ অব্দ) রচিত মানসোল্লাস’ গ্রন্থের ‘গীত-বিনোদ’ অধ্যায়ে বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় রচিত গীতের দৃষ্টান্ত আছে। ইহার মধ্যে বিষ্ণুর অবতার ও গোপীগণের সহিত কৃষ্ণের লীলাবিষয়ক কয়েকটি বাংলা গীতের অংশ আছে। গীতগোবিন্দের রচনাভঙ্গী যে প্রাচীন বাংলা ও অপভ্রংশে রচিত গীতিকবিতার অনুরূপ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি জনপ্রিয় সংস্কৃত মহাকাব্য অবলম্বনে যে বাংলা ভাষায় একটি লৌকিক সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল ইহাও খুবই সম্ভব। কিন্তু এরূপ রচনার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। মোটের উপর একথা বলা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধ সহজিয়া মতের চর্য্যাপদগুলি ছাড়া প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত এমন আর কিছুই পাওয়া যায় নাই, যাহা দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেকার বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। মধ্যযুগে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রভাবে যে বাংলা সাহিত্যের অপূৰ্ব্ব পরিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল, সম্ভবত পুরাতন বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম্মের প্রভাবেই সেই সাহিত্যের প্রথম সৃষ্টি হয়। পণ্ডিত ও প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষকগণ সংস্কৃতকেই একমাত্র সাধুভাষা ও সাহিত্যের বাহন মনে করিতেন, কিন্তু নূতন ও অর্ব্বাচীন ধর্ম্মমত জনসাধারণে প্রচলিত করার জন্য ইহার আচাৰ্য্যগণ জনসাধারণের ভাষায়ই ইহাকে প্রচার করিতে যত্নবান ছিলেন। ইহাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সৃষ্টি ও পরিপুষ্টির প্রধান কারণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।
.
৫. বাংলা লিপি
অনেকের বিশ্বাস যে প্রাচীনকালেও সংস্কৃত ভাষা নাগরী অক্ষরেই লিখিত হইত, এবং বাংলা ভাষার ন্যায় বাংলায় প্রচলিত অক্ষরগুলিও অপেক্ষাকৃত আধুনিক। কিন্তু এই দুইটি মতই ভ্রান্ত। সর্বত্রই সংস্কৃত, প্রাকৃত ও দেশীয় ভাষা সবই একরকম অক্ষরে লিখিত হইত, এবং দেশ ও কাল অনুসারে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন রূপ ছিল। কেবলমাত্র সংস্কৃত লেখার জন্য কোনো পৃথক অক্ষর ব্যবহৃত হইত না।
মৌৰ্য্যসম্রাট অশোক খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে যে ব্রাহ্মী লিপিতে তাঁহার অধিকাংশ শাসনমালা উত্তীর্ণ করান তাহা হইতেই ক্রমে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন বর্ণমালার উদ্ভব হইয়াছে। সম্রাট অশোকের সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ব্যতীত আর সৰ্ব্বত্রই এই এক প্রকার লিপিরই প্রচলন ছিল। কালক্রমে ও স্থানীয় লোকের বিভিন্ন রুচি অনুযায়ী বিভিন্ন প্রদেশে ইহার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। এই সমুদয় পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও গুপ্তযুগের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমুদয় বিভিন্ন বর্ণমালা প্রচলিত ছিল তাহাদের মধ্যে প্রভেদ খুব বেশী ছিল না। এক দেশের লোক অন্য দেশের বর্ণমালা পড়িতে পারিত।
গুপ্তযুগেই প্রথম প্রাদেশিক বর্ণমালার মধ্যে স্বাতন্ত্র ও প্রভেদ বাড়িয়া উঠে। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে পূর্ব্ব ভারতের ও পশ্চিম ভারতের বর্ণমালা দুইটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি অবলম্বন করে। পশ্চিম ভারতের সিদ্ধমাতৃকা-বর্ণমালা ক্রমশ রূপান্তর হইতে হইতে নাগরীতে পরিণত হয়। আর পূর্ব্ব ভারতের বর্ণমালা হইতেই অবশেষে বাংলা বর্ণমালার উৎপত্তি হয়।
সমাচার দেবের কোটালিপাড়া তাম্রশাসনে পূর্ব্ব ভারতে প্রচলিত এই বিশিষ্ট পদ্ধতির বর্ণমালার নিদর্শন পাওয়া যায়। সপ্তম হইতে নবম শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহার ক্রমশ অনেক পরিবর্ত্তন হয়। দশম শতাব্দীতে পশ্চিম ভারতের বর্ণমালা ইহার উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু ঐ শতাব্দের শেষভাগে প্রথম মহীপালের রাজত্বে এই প্রভাব দূর হয়, এবং পূৰ্ব্ব ভারতীয় বর্ণমালায় বাংলা বর্ণমালার পূৰ্ব্বাভাস পাওয়া যায়। প্রথম মহীপালের বাণগড়-লিপিতে ব্যবহৃত অ, উ, ক, খ, গ, ধ, ন, ম, ল এবং ক্ষ অনেকটা বাংলা অক্ষরের আকার ধারণ করিয়াছে। জ একেবারে সম্পূর্ণ বাংলা জ’য়ের অনুরূপ। দ্বাদশ শতাব্দীতে উত্তীর্ণ বিজয়সেনের দেওপাড়া-প্রশস্তিতে যে বর্ণমালা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাঁহার মধ্যে ২২টি পুরাপুরি অথবা প্রায় বাংলা অক্ষরের মতন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে এবং এয়োদশ শতাব্দের প্রথমে তাম্রশাসনের অক্ষর প্রায় সম্পূর্ণ আধুনিক বাংলা অক্ষরে পরিণত হইয়াছে। ইহার পর তিন-চারিশত বত্সর পর্য্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে এই অক্ষরের কিছু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে পরিবর্ত্তন বিশেষ কিছু হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনের ফলে বাংলা অক্ষরগুলি একটি নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করিয়াছে। ভবিষ্যতে ইহার আর কোনোরূপ পরিবর্ত্তন হইবে বলিয়া মনে হয় না। এইরূপে দেখা যায় যে গুপ্তযুগের পরবর্ত্তীকালে বাংলায় যখন একটি স্বাধীন পরাক্রান্ত রাজ্য স্থাপিত হয়, সেই সময় হইতেই পূৰ্ব্ব ভারতে একটি বিশিষ্ট বর্ণমালার প্রচলন হয়। ক্রমে এই বর্ণমালা পরিবর্তিত হইয়া বাংলার নিজস্ব একটি বর্ণমালায় পরিণত হয়। বলা বাহুল্য যে চিরকালই বাংলার প্রচলিত অক্ষরেই বাংলায় সংস্কৃত, প্রাকৃত ও দেশীয় ভাষা প্রভৃতি লিখিত হয়। সংস্কৃত ভাষা লিখিবার জন্য নাগরী অক্ষরের ব্যবহার অতি আধুনিক কালেই হইয়াছে। প্রাচীন বাংলার সংস্কৃত ভাষায় লিখিত সমুদয় তাম্রশাসন ও পুঁথিই তকালে প্রচলিত বাংলা অক্ষরেই লেখা হইয়াছে। আর নাগরী অক্ষর বাংলা অপেক্ষা প্রাচীন নহে; অর্থাৎ দশম শতাব্দীতে বাংলা দেশে ব্যবহৃত অক্ষরের সহিত বর্ত্তমান বাংলা অক্ষরের যে সম্বন্ধ, ঐ সময়ে পশ্চিম ভারতে ব্যবহৃত অক্ষরের সহিত বর্ত্তমান নাগরী অক্ষরের সম্বন্ধ তদপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্ঠ নহে।
১৭. ধৰ্ম্মমত ও দেব-দেবীর মূর্ত্তি পরিচয়
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ
প্রথম খণ্ড-ধৰ্ম্মমত
১. আৰ্য্যধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা
আৰ্যগণের সংস্পর্শে ও প্রভাবে তাঁহাদের ধর্ম্মগত ও সামাজিক রীতিনীতি ক্রমে ক্রমে বাংলায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। খৃষ্টপূৰ্ব চতুর্থ শতাব্দের শেষ ভাগে যখন আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন তখন গঙ্গাসাগরসঙ্গম হইতে পঞ্চনদের পূৰ্ব্বসীমা পর্য্যন্ত ভূভাগ এক অখণ্ড বিরাট রাজ্যের অধীন ছিল। সুতরাং এই সময়ে যে বাংলায় আৰ্যপ্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বৌধায়ন-ধৰ্ম্মসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রমাণিত হয় যে তখনো বাংলা দেশে আৰ্য সভ্যতা বিস্তৃত হয় নাই। সুতরাং খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ ও চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যে আৰ্য সভ্যতা বাংলায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।
ইহার পূর্ব্বে যাঁহারা বাংলায় বাস করিতেন, তাঁহাদের ধর্ম্মমত কিরূপ ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। কারণ ঐতিহাসিক যুগে তাহারা সকলেই বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য প্রভৃতি আৰ্য্যগণের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তবে ইহা খুবই সম্ভব যে তাঁহাদের প্রাচীন ধর্ম্মমত, সংস্কার, পূজাপদ্ধতি প্রভৃতি রূপান্তরিত হইয়া আৰ্য্য ধৰ্ম্মের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের যে গুরুতর প্রভেদ দেখা যায়, সম্ভবত প্রাচীন অধিবাসীগণের ধর্ম্ম ও সংস্কারের প্রভাব তাঁহার অন্যতম কারণ। বর্ত্তমানকালে বাংলায় ও ভারতের অন্যান্য দেশে প্রচলিত ধর্ম্ম অনুষ্ঠানের মধ্যে অনেক প্রভেদ দেখা যায়। অসম্ভব নহে যে ইহা অন্তত কতকাংশে বাংলার প্রাচীন অধিবাসীদিগের আচার-অনুষ্ঠানের প্রভাবের ফল। কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেও প্রাচীন বাঙ্গালীর ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা করা যায় না। সুতরাং বাংলায় আৰ্য্য ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে যে ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল তাঁহার কোনো বিবরণ দেওয়া সম্ভবপর নহে। আর্য্য সভ্যতার প্রভাবে খুব প্রাচীনকালেই বাংলায় বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু গুপ্তযুগের অর্থাৎ খৃষ্টীয় চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বে বাংলার এই সমুদয় ধৰ্ম্ম সম্বন্ধে বিস্তৃত কোনো বিবরণ জানিবার উপায় নাই।
.
২. বৈদিক ধর্ম্ম
গুপ্তযুগের তাম্রশাসনগুলি হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে বৈদিক যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া বাংলায় বহুল পরিমাণে অনুষ্ঠিত হইত। এই সমুদয় তাম্রশাসনে অগ্নিহোত্র ও পঞ্চ মহাযজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠান এবং মন্দির নির্মাণ ও দেব-দেবীর পূজার ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদানের উল্লেখ আছে। এই সমুদয় ব্রাহ্মণদিগের পরিচয় প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে যে তাঁহারা ঋক, যজু অথবা সামবেদ অধ্যয়ন করিতেন। ভূমিদান করিয়া ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠা করা বিশেষ পুণ্যের কাৰ্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত এবং একখানি তাম্রশাসনে বাংলার পূর্ব্ব সীমান্তে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুসমাকুল নিবিড় অরণ্য প্রদেশেও মন্দির নির্মাণ এবং বহুসংখ্যক বেদজ্ঞ প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। উত্তরে হিমালয় শিখরেও মন্দির নির্ম্মিত হইত। সুতরাং সমস্ত বাংলা দেশেই যে গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের, বিশেষত বৈদিক অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল যে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মার নিধানপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে শ্রীহট্ট অঞ্চলে খৃষ্টীয় ষষ্ট শতাব্দীতে ভূমিদানপূর্ব্বক ২০০৫ জন ব্রাহ্মণের প্রতিষ্ঠার কথা লিখিত আছে। এই ব্রাহ্মণগণের বিভিন্ন বৈদিক শাখা ও গোত্রের নামও উল্লিখিত হইয়াছে। রাতবংশীয় রাজগণের সময়েও কুমিল্লা অঞ্চলে বহু ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করা হইয়াছিল।
পালরাজগণের তাম্রশাসনেও বেদ, বেদাঙ্গ, মীমাংসা প্রভৃতিতে ব্যুৎপন্ন এবং বৈদিক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ বংশের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। বৰ্ম ও সেনরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বৈদিক ধর্ম্ম বাংলায় আরও প্রসার লাভ করে। ভট্টভবদেবের প্রশস্তিতে বেদবিদ, সাবর্ণ গোত্র ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত শত গ্রামের উল্লেখ আছে। বৰ্ম্মরাজগণ বৈদিক ধর্ম্মের রক্ষক বলিয়া তাম্রশাসনে অভিহিত হইয়াছেন। ব্রহ্মবাদী সামন্তসেন শেষ বয়সে যজ্ঞধূমে পরিপূর্ণ গঙ্গাতীরস্থিত পবিত্র ঋষির আশ্রমে বাস করিতেন। সমসাময়িক লিপির এই সমুদয় উক্তি হইতে প্রমাণিত হয় যে গুপ্তযুগ হইতে হিন্দু যুগের শেষ পর্য্যন্ত বাংলায় বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত। সেনযুগে রচিত কয়েকখানি গ্রন্থও এই অনুমানের সমর্থন করে।
তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, মধ্যদেশ হইতে আসিয়া কোনো কোনো বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বাংলা দেশে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা হইতে এরূপ মনে করিবার কারণ নাই যে বাংলা দেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব ছিল। কারণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষের এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে যাইয়া বাস স্থাপন করিয়াছেন, এরূপ বহু দৃষ্টান্ত তাম্রশাসন হইতে জানা যায়। বাংলা দেশ হইতে বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের দেশান্তরে গমনের কথা তাম্রশাসনে পাওয়া যায়। এদেশে একটি জনশ্রুতি বিশেষভাবে প্রচলিত আছে যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব হওয়ায় রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, বাংলার রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ, অর্থাৎ বৈদিক প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় ব্যতীত প্রায় সকল ব্রাহ্মণই, তাঁহাদের বংশসম্ভূত। পূৰ্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা এই মতের সম্পূর্ণ বিরোধী, এবং বাংলায় যে গুপ্তযুগের পরবর্ত্তী কোনোকালে বৈদিক অনুষ্ঠানে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণের একেবারে অভাব ছিল, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। তবে হয়তো ভারতবর্ষের অন্য কোনো কোনো প্রদেশের তুলনায় বাংলায় বৈদিক চর্চ্চা খুবই কম হইত। পালযুগে বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবের কথা স্মরণ করিলে ইহাই খুব সম্ভব বলিয়া মনে হয়।
কুলশাস্ত্রমতে যে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ বৈদিক অনুষ্ঠানের জন্য এদেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, পণ্ডিতপ্রবর হলায়ূধ স্পষ্টত তাঁহাদেরই বৈদিক জ্ঞানের অভাবের উল্লেখ করিয়াছেন। হলায়ুধের উক্তি হইতে প্রমাণিত হয় যে (সম্ভবত অন্য প্রদেশের তুলনায়) তাঁহার কালে বাংলায় বৈদিক জ্ঞানের খুব প্রসার ছিল না, এবং কোনো কোনো শ্রেণীর ব্রাহ্মণের এ বিষয়ে যথেষ্ট শৈথিল্য ছিল। কিন্তু তাঁহার সময়েও যে বাংলায় বেদের পঠনপাঠন ও বৈদিক অনুষ্ঠান বিশেষভাবেই প্রচলিত ছিল তাঁহার নিজের জীবনী এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।
.
৩. পৌরাণিক ধৰ্ম্ম
ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় গুপ্তযুগে বাংলায় পৌরাণিক ধৰ্ম্মের যথেষ্ট প্রসার ছিল। বাংলায় যে সমুদয় তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে অনেক পৌরাণিক দেব-দেবী ও তাঁহাদের বহু আখ্যান পাওয়া যায়। দেবরাজ ইন্দ্র অথবা পুরন্দর, এবং দৈত্যরাজ বলির হস্তে তাঁহার পরাজয়; বিষ্ণু (হরি, মুরারি), লক্ষ্মী এবং তাঁহাদের বাহন গরুড়; বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি, সত্যযুগে বলি এবং দ্বাপরে কর্ণের দানশীলতা; অগস্ত্য কর্ত্তৃক সমুদ্রপান; পরশুরাম কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়কুল সংহার; রামচন্দ্রের বীরত্ব; পৃথু, সগর, নল, ধনঞ্জয়, যযাতি ও অম্বরীষ প্রভৃতির কাহিনী,-এই সমুদয় তাম্রশাসনে পুনঃপুন উল্লিখিত হইয়াছে।
বাংলায় যে বৈষ্ণব ও শৈবধর্ম্মের বিশেষ প্রসার ছিল তাহাও এই সমুদয় তাম্রশাসন হইতে জানা যায়। ভাগবত সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা বিষ্ণু কৃষ্ণে রূপান্তরিত হইয়াছেন। কৃষ্ণের জন্ম ও বাল্যলীলা, বিশেষত গোপীদিগের সহিত ক্রীড়া প্রভৃতির অনেক প্রসঙ্গ আছে-এবং তিনি যে বিষ্ণুর অবতার তাঁহারও উল্লেখ আছে। বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারগণেরও নাম ও কীর্তি বর্ণিত হইয়াছে। শিবের ভিন্ন ভিন্ন নাম (যথা সদাশিব, অর্দ্ধনারীশ্বর, ধুর্জটি ও মহেশ্বর); তাঁহার শক্তি সর্বাণী, উমা অথবা সতী; দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ; কার্ত্তিক গণেশ নামে তাঁহার দুই পুত্র প্রভৃতিরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমুদয় দেব-দেবীর মূর্ত্তির সংখ্যা ও গঠনপ্রণালীর বিভিন্নতা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, বাংলায় ইহাদের পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল এবং উপাসকগণ বহুসংখ্যক বিশিষ্ট সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন।
.
৪. বৈষ্ণব ধর্ম্ম
বাঁকুড়া নগরীর ১২ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত সুসুনিয়া নামক পৰ্ব্বতের গুহায় উৎকীর্ণ রাজা চন্দ্রবর্ম্মার একখানি লিপিতে বাংলায় সর্বপ্রথমে বিষ্ণুপূজার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই গুহাগাত্রে একটি চক্র খোদিত আছে। সুতারং অনুমিত হয় যে ইহা একটি বিষ্ণুর মন্দির ছিল। রাজা চন্দ্রবর্ম্মা চতুর্থ শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গে, এবং এমনকি সুদূর হিমালয় শিখরে গোবিন্দস্বামী, শ্বেতবরাহস্বামী, কোকামুখস্বামী প্রভৃতির মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্ভবত এ সমুদয়ই বিষ্ণুমূর্ত্তি। সপ্তম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ লিপিতে বাংলার পূর্ব্বপ্রান্তে হিংস্রপশুসমাকুল গভীর অরণ্য প্রদেশও ভগবান অনন্তনারায়ণের মন্দির ও পূজার উল্লেখ আছে। সুতরাং ইহার বহু পূর্ব্বেই যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বাংলার সর্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।
বাংলার বৈষ্ণব ধৰ্ম্মে কৃষ্ণলীলার বিশেষ প্রাধান্য ছিল। পাহাড়পুর মন্দিরগাত্রে কৃষ্ণের বাল্যলীলার অনেক কাহিনী উত্তীর্ণ আছে। সদ্যপ্রসূত কৃষ্ণকে লইয়া বসুদেবের গোকুলে গমন, গোপগোপীগণের সহিত ক্রীড়া, গোবর্দ্ধনধারণ, যমলাৰ্জ্জুন সংহার, কেশীবধ, চানুর ও মুষ্টিকের সহিত যুদ্ধ প্রভৃতি কাহিনী যে ষষ্ঠ শতাব্দী বা তাঁহার পূর্ব্বেই এদেশে প্রচলিত ছিল পাহাড়পুরের প্রস্তরশিল্প হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। একখানি প্রস্তরে কৃষ্ণ ও একটি স্ত্রীমূর্ত্তি খোদিত আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে ইহা রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তি। পরবর্ত্তীকালে রাধা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে প্রাধান্য লাভ করিলেও হালের সপ্তশতী ব্যতীত প্রাচীন কোনো গ্রন্থে রাধার উল্লেখ নাই। পাহাড়পুরে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূৰ্ত্তি থাকিলে বাংলায় ইহাই রাধার আখ্যানের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন। কিন্তু খুব সম্ভবত পাহাড়পুরের উক্ত স্ত্রীমূর্ত্তি রুক্সিণী অথবা সত্যভামা। সুতরাং সপ্তম শতাব্দীতে কৃষ্ণলীলা বাংলায় খুব জনপ্রিয় হইলেও ঐ সময়ে রাধা-কৃষ্ণের কাহিনী প্রচলিত ছিল কি না তাহা নিঃসংশয়ে বলা যায় না।
অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল ঐযুগের বহুসংখ্যক বিষ্ণুমূৰ্ত্তি হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। রাজা লক্ষ্মণসেন পরম বৈষ্ণব ছিলেন এবং তাঁহার সময় হইতে রাজকীয় শাসনের প্রারম্ভে শিবের পরিবর্তে বিষ্ণুর স্তবের প্রচলন হয়। তাঁহার সভাকবি জয়দেবের গীতগোবিন্দ যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে বিশেষ সম্মানীত ও আদৃত তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। গীতগোবিন্দে যে বিষ্ণুর দশ অবতারের বর্ণনা আছে কালে তাহাই সমগ্র ভারতে গৃহীত হইয়াছে। ইহার পূৰ্ব্বে অবতার সম্বন্ধে কোনো নির্দিষ্ট বা সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। ভাগবত পুরাণে অবতারের যে তিনটি তালিকা আছে তাহাতে অবতারের সংখ্যা যথাক্রমে ২২, ২৩ ও ১৬। হরিবংশে দশ অবতারের উল্লেখ থাকিলেও তাঁহার সহিত জয়দেবের কথিত এবং বর্ত্তমানে প্রচলিত দশ অবতারের অনেক প্রভেদ। মহাভারত ও বায়ুপুরাণে এই দশ অবতারের তালিকা আছে-কিন্তু তাঁহার পাশেই বিভিন্ন তালিকাও দেওয়া হইয়াছে। জয়দেব বর্ণিত যে অবতারবাদ ক্রমে ভারতের সর্বত্র প্রামাণিক বলিয়া গৃহীত হইয়াছে তাহা ভারতে বাংলার বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি প্রধান দান বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। জয়দেব বর্ণিত রাধাকৃষ্ণ লীলাও সম্ভবত বাংলায়ই প্রথমে প্রচলিত হয় ও পরে সমগ্র ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করে।
.
৫. শৈবধর্ম্ম
বৈষ্ণব ধর্ম্মের ন্যায় শৈবধৰ্ম্মও গুপ্তযুগে এদেশে প্রচলিত ছিল। পঞ্চম শতাব্দের লিপিতে হিমালয় গিরিশিখরে পূর্ব্বোক্ত শ্বেতবরাহস্বামী ও কোকামুখ স্বামীর মন্দির পার্শ্বে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার উল্লেখ পাওয়া যায়। ষষ্ঠ শতাব্দীতে মহারাজ বৈন্যগুপ্ত ও সপ্তম শতাব্দীতে মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক ও ভাস্করবর্ম্মা শৈবধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রে শিবের কয়েকটি মূর্ত্তি উত্তীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।
আর্য্যাবর্তে পাশুপত মতাবলম্বীরাই সর্বপ্রাচীন শৈব-সম্প্রদায়। সম্রাট নারায়ণপালের একখানি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি নিজে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তথাকার পাশুপতাচাৰ্য্য-পরিষদের ব্যবহারের জন্য একটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, বাংলায় পাশুপত-সম্প্রদায় খুব প্রবল ছিল। সদাশিব সেনরাজগণের ইষ্টদেবতা ছিলেন এবং রাজকীয় মুদ্রায় তাঁহার মূর্ত্তি উত্তীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। বিজয়সেন ও বল্লালসেন শৈব ছিলেন। লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার বংশধরগণ বৈষ্ণব হইলেও কুলদেবতা সদাশিবকে পরিত্যাগ করেন নাই।
খুব প্রাচীনকাল হইতেই বাংলায় শক্তিপূজার প্রচলন হইয়াছিল। দেবীপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, রাঢ় ও বরেন্দ্রে বামাচারী শাক্ত সম্প্রদায় বিভিন্নরূপে দেবীর উপাসনা করিতেন। দেবীপুরাণ সম্ভবত সপ্তম শতাব্দের শেষে অথবা অষ্টম শতাব্দের প্রারম্ভে রচিত হইয়াছিল। বাংলার বহু তান্ত্রিক গ্রন্থে শাক্ত মত প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু এই শ্রেণীর কোনো গ্রন্থ দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল কি না বলা কঠিন। তবে তন্ত্রোক্ত শাক্তমত যে হিন্দু যুগ শেষ হইবার পূর্ব্বেই বাংলায় প্রসার লাভ করিয়াছিল ইহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি বাম হস্তে মস্তকের শিখা ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে তরবারির দ্বারা নিজের গ্রীবাদেশ কাটিতে উদ্যত এরূপ একটি দৃশ্য উত্তীর্ণ আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইহা দেবীর নিকট শাক্তভক্তের শিরশ্চেদের দৃশ্য। সুতরাং ইহা সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীতে শাক্ত-সম্প্রদায়ের অস্তিত্বের প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে।
.
৬. অন্যান্য পৌরাণিক ধৰ্ম্ম-সম্প্রদায়
বিষ্ণু, শিব ও শক্তি ব্যতীত অন্যান্য পৌরাণিক দেব-দেবীর পূজাও বাংলায় প্রচলিত ছিল। কিন্তু এইসব সম্প্রদায় সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। রাজতরঙ্গিণীতে উক্ত হইয়াছে যে, পুণ্ড্রবর্দ্ধনে কার্তিকের এক মন্দির ছিল। কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেন তাঁহাদের তাম্রশাসনে পরমসৌর বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। সুতরাং সূৰ্য্য-দেবতার উপাসক সৌর সম্প্রদায় বাংলায় প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এই সূৰ্য্য বৈদিক সূৰ্য্য দেবতা নহেন। সম্ভবত মগ ব্রাহ্মণগণ কুশাণযুগে শকদ্বীপ হইতে এই সূৰ্য্যপূজার প্রচলন করেন।
কিন্তু সমসাময়িক লিপি বা সাহিত্যে অন্য সম্প্রদায়ের উল্লেখ না থাকিলেও বাংলায় কার্তিক ও সূৰ্য্য ব্যতীত অন্যান্য দেব-দেবীর বহুসংখ্যক মূৰ্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুতরাং ইহাদের পূজাও যে এদেশে প্রচলিত ছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়।
.
৭. জৈনধর্ম্ম
প্রাচীন জৈনধর্ম্মগ্রন্থে লিখিত আছে যে, বর্দ্ধমান মহাবীর রাঢ় প্রদেশে আসিয়াছিলেন, কিন্তু সেখানকার লোকেরা তাঁহার সহিত অত্যন্ত অসদ্ব্যবহার করিয়াছিল। কোন সময়ে জৈনধৰ্ম্ম বাংলায় প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তাহা সঠিক বলা যায় না। দিব্যাবদানে আশোকের সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীর জৈনগণ মহাবীরের চরণতলে পতিত বুদ্ধদেবের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে শুনিয়া তিনি নাকি পাটলিপুত্রের সমস্ত জৈনগণকে হত্যা করিয়াছিলেন। এই গল্পটির মূলে কতটা সত্য আছে বলা কঠিন-সুতরাং আশোকের সময়ে উত্তরবঙ্গে জৈন-সম্প্রদায় বর্ত্তমান ছিল এরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত নহে।
কিন্তু অশোকের সময় না থাকিলেও খৃষ্টপূৰ্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে যে বঙ্গে জৈনধৰ্ম্ম দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাঁহার প্রমাণ আছে। প্রাচীন জৈনগ্রন্থ কল্পসূত্র মতে মৌৰ্য্যম্রাট চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক জৈন আচাৰ্য্য দ্রবাহুল্য শিষ্য গোদাস যে গোদাসগণ প্রতিষ্ঠিত করেন, কালক্রমে তাহা চারি শাখায় বিভক্ত হয়। ইহার তিনটির নাম তাম্রলিপ্তিক, কোটীবর্ষীয় এবং পুণ্ড্রবর্দ্ধনীয়। এই তিনটি যে বাংলার তিনটি সুপরিচিত নগরীর নাম হইতে উদ্ভূত তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কল্পসূত্রোক্ত এই শাখাগুলি কাল্পনিক নহে, সত্য-সত্যই ছিল, কারণ খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে উত্তীর্ণ শিলালিপিতে তাহাদের উল্লেখ আছে। সুতরাং উত্তরবঙ্গ (পুণ্ড্রবর্দ্ধন, কোটীবর্ষ) ও দক্ষিণবঙ্গে (তাম্রলিপ্তি) যে খুব প্রাচীনকাল হইতেই জৈন সম্প্রদায় প্রসার লাভ করিয়াছিল তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই।
পাহাড়পুরে প্রাপ্ত একখানি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বা তাঁহার পূর্ব্বে ঐ স্থানে একটি জৈনবিহার ছিল। চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন সাং লিখিয়াছেন যে, তাঁহার সময়ে বাংলায় দিগম্বর জৈনের সংখ্যা খুব বেশি ছিল। কিন্তু তাঁহার পরই বাংলায় জৈনধৰ্ম্মের প্রভাব হ্রাস হয়। পাল ও সেনরাজগণের তাম্রশাসনে এই সম্প্রদায়ের কোনো উল্লেখ নাই। তবে ইহা যে একেবারে লুপ্ত হয় নাই, প্রাচীন জৈনমূৰ্ত্তি হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়।
.
৮. বৌদ্ধধর্ম্ম
সম্রাট অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম্ম বাংলায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বেও সম্ভবত এদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার হইয়াছিল, তবে এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে উত্তীর্ণ একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল।
পঞ্চম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম বাংলায় বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ফাহিয়ান লিখিয়াছেন যে, তখন তাম্রলিপ্তি নগরীতে ২২টি বৌদ্ধবিহার ছিল। তিনি তথায় দুই বৎসর থাকিয়া বৌদ্ধ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এবং বুদ্ধমূর্ত্তির ছবি আঁকিয়াছিলেন। তাঁহার বিস্তৃত বর্ণনায় তাম্রলিপ্তির বিশাল বৌদ্ধ সংঘের একটি উজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছিল।
৫০৬-৭ অব্দে উত্তীর্ণ একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, কুমিল্লা অঞ্চলে তখন বহু বৌদ্ধবিহার ছিল। তাঁহার মধ্যে একটির নাম রাজবিহার; সম্ভবত কোনো রাজা কর্ত্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং পঞ্চম শতাব্দীতে বাংলার সর্বত্রই যে বৌদ্ধধর্ম্মের খুব প্রতিপত্তি ছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।
সপ্তম শতাব্দীতে বাংলায় যে বৌদ্ধধর্ম্ম বেশ প্রভাবশালী ছিল, বহু চীনদেশীয় পরিব্রাজকের উক্তি হইতে তাহা জানা যায়। ইঁহাদের মধ্যে হুয়েন সাংয়ের বিবরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহার সারমর্ম নিম্নে দিতেছি।
“কজঙ্গল (রাজমহলের নিকটবর্ত্তী) প্রদেশে ছয়-সাতটি বিহারে তিন শতেরও অধিক ভিক্ষু বাস করেন। অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের দশটি মন্দির আছে। এই প্রদেশের উত্তর ভাগে গঙ্গাতীরের নিকট বিশাল উচ্চ দেবালয় আছে। ইহা প্রস্তর ও ইষ্টকে নির্ম্মিত এবং ইহার ভিত্তি-গাত্রে ক্ষোদিত ভাস্কৰ্য্য উচ্চ শিল্পকলার নিদর্শন। চতুর্দিকের দেয়ালে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বুদ্ধ, অন্যান্য দেবতা ও সাধু পুরুষদের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ।”
“পুণ্ড্রবর্দ্ধনে (উত্তরবঙ্গ) ২০টি বিহারে তিন শতেরও অধিক হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রায় একশত দেবমন্দির আছে। উলঙ্গ নিগ্রন্থপন্থীদের (জৈন) সংখ্যা খুব বেশী। রাজধানীর তিন-চারি মাইল পশ্চিমে পো-চি-পো সংঘারাম। ইহার অঙ্গনগুলি যেমন প্রশস্ত, কক্ষ ও শিখরগুলিও তেমনি উচ্চ। ইহার ভিক্ষুসংখ্যা ৭০০। সকলেই মহাযান মতাবলম্বী। পূর্ব্ব ভারতের বহু প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ আচার্য্য এখানে বাস করেন। সমতট (পূর্ব্ববঙ্গ) প্রদেশের রাজধানীতে প্রায় ৩০টি বৌদ্ধবিহারে ২০০০ ভিক্ষু থাকেন। অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মন্দিরের সংখ্যা একশত। জৈনগণ সংখ্যায় খুব বেশী। তাম্রলিপ্তে দশটি বিহারে সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করেন। অন্যান্য সম্প্রদায়ের মন্দিরসংখ্যা পঞ্চাশ। কর্ণসুবর্ণে দশটি বৌদ্ধবিহারে হীনযান মতাবলম্বী দুই সহস্র ভিক্ষু বাস করেন। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা খুব বেশী-তাহাদের দেবমন্দিরের সংখ্যা পঞ্চাশ। রাজধানীর নিকটে লো-টো-বি-চি বিহার। ইহার কক্ষগুলি প্রশস্ত ও উচ্চ। বহুতালায় নির্ম্মিত বিহারটিও খুব উচ্চ। রাজ্যের সমুদয় সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ এখানে সমবেত হন।”
এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, তখন বাংলায় বৈষ্ণব, শৈব, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভৃতি বিবিধ ধৰ্ম্ম-সম্প্রদায়ের বহুসংখ্যক মন্দির ও বিহার বর্ত্তমান ছিল। জৈন ভিক্ষুগণ সংখ্যায় বৌদ্ধ ভিক্ষু অপেক্ষা বেশী ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। বৌদ্ধগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ না হইলেও বাংলায় বৌদ্ধধর্ম্মের বেশ প্রভাব ছিল। ইৎসিং তাম্রলিপ্তির বৌদ্ধবিহারের যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, তথাকার ভিক্ষুগণের জীবন বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও বিধিবিধানের সম্পূর্ণ অনুবর্ত্তী ছিল। শেংচি নামে ইৎসিংয়ের সমসাময়িক আর একজন চীনদেশীয় বৌদ্ধ পরিব্রাজক লিখিয়াছেন যে, সমতটের রাজধানীতে চারি সহস্রের বেশী বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী ছিলেন এবং ঐ দেশের রাজা রাজভট প্রতিদিন বুদ্ধের লক্ষ মৃন্ময়মূৰ্ত্তি নিৰ্মাণ করিতেন এবং মহাপ্রজ্ঞাপারমিতার লক্ষ শ্লোক পাঠ করিতেন। রাজভট সম্ভবত খড়গবংশীয় রাজা ছিলেন। এই সমুদয় বর্ণনা হইতে বেশ বোঝা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্ম বাংলায় খুব শক্তিশালী ছিল এবং বাংলার বৌদ্ধগণ জ্ঞান, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও আচার-ব্যবহারে সমগ্র বৌদ্ধজগতের শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র হইয়াছিলেন।
সপ্তম শতাব্দীতে একজন বাঙ্গালী বৌদ্ধজগতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার নাম শীলভদ্র-সমতটের রাজবংশে হঁহার জন্ম হয়। ইনি জগদ্বিখ্যাত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য্য ও সর্বাধ্যক্ষের পদ অলঙ্কত করিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। ইহার জীবনী একবিংশ পরিচ্ছেদে আলোচিত হইবে।
অষ্টম শতাব্দীতে বৌদ্ধ পালরাজগণের অভ্যুদয়ে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এই সময় হইতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশ ক্ষীণবল হইয়া আসিতেছিল এবং দুই-এক শত বৎসরের মধ্যেই তাঁহার প্রভাব প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু পালরাজগণের সুদীর্ঘ চারিশত বৎসর রাজত্বকালে বাংলা ও বিহারে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ তুর্কী আক্রমণের ফলে যখন প্রথমে মগধের ও পরে উত্তর বাংলার বৌদ্ধবিহার ও মন্দিরগুলি ধ্বংস হয়, তখনই বৌদ্ধ সংঘ ভারতের পূর্ব্ব-প্রান্তস্থিত এই সর্ব্বশেষ আশ্রয়স্থান হইতে বিতাড়িত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য নেপাল ও তিব্বতে গমন করে। বৌদ্ধ সংঘই ছিল বৌদ্ধধর্ম্মের প্রধান কেন্দ্র। কাজেই বৌদ্ধ সংঘের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মও ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হয়।
অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দের মধ্যে বাংলায় ও বিহারে বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। এই চারিশত বৎসরে ইহা উত্তরে তিব্বত ও দক্ষিণে যবদ্বীপ, সুমাত্রা, মালয় প্রভৃতি অঞ্চলে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল! বাংলার পালরাজগণ ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ রক্ষক হিসেবে সমগ্র বৌদ্ধজগতে শ্রেষ্ঠ সম্মানের আসন পাইয়াছিলেন। ইহার ফলে বাংলায় ও বিহারে বৌদ্ধধর্ম্মের যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, তাহা এই সমুদয় দেশেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বাংলা ও বিহারের প্রসিদ্ধ আচাৰ্য্যগণ এই সমুদয় দেশে গিয়া এই নতুন ধর্ম্মের ভিত্তি দৃঢ় করিয়াছিলেন।
পাল সম্রাটগণ বহু বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ধর্ম্মপাল প্রতিষ্ঠিত বিক্রমশীল মহাবিহারই সমধিক প্রসিদ্ধ। ভাগীরথী তীরে এক গিরিশীর্ষে এই মহাবিহারটি অবস্থিত ছিল। বর্ত্তমান পাথরঘাটায় (ভাগলপুর জিলা) কেহ কেহ ইহার অবস্থিতি নির্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। ধর্ম্মপাল প্রতিষ্ঠিত এই মহাবিহার এবং সোমপুর ও ওদন্তপুরী বিহারের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, সুতরাং এ স্থলে ইহাদের বর্ণনা অনাবশ্যক।
সোমপুর ব্যতীত বাংলায় আরও কয়েকটি প্রসিদ্ধ বিহার ছিল। যে ত্রৈকূটক বিহারে আচাৰ্য্য হরিদ্র অভিসময়ালঙ্কার গ্রন্থের প্রসিদ্ধ টীকা প্রণয়ন করেন, তাহা সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত ছিল। বরেন্দ্রের দেবীকোট ও জগদ্দল, চট্টগ্রামের পণ্ডিতবিহার, এবং বিক্রমপুর ও পট্টিকেরা (কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী) প্রভৃতি বৌদ্ধবিহারে যে সমুদয় বৌদ্ধ আচার্য্য ছিলেন, তাঁহাদের অনেকে তিব্বতীয় বৌদ্ধ সাহিত্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।
পালযুগে বাংলায় অন্যান্য বৌদ্ধরাজবংশেরও পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিক্রমপুরের চন্দ্ররাজবংশ এবং হরিকেলরাজ কান্তিদেবের উল্লেখ করা যাইতে পারে। সেনরাজগণের অভ্যুদয়ের ফলে বাংলায় শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম এবং প্রাচীন বৈদিক ও পৌরাণিক ধৰ্ম্মানুষ্ঠান ও আচার-ব্যবহার পুনরুজ্জীবিত করিবার এক প্রবল চেষ্টা হয়। ইহাও বাংলায় বৌদ্ধধর্ম্মের পতনের একটি কারণ। কিন্তু তুর্কী আক্রমণের ফলে বৌদ্ধবিহারগুলি ধ্বংস না হইলে সম্ভবত বৌদ্ধধর্ম্ম বাংলা হইতে একেবারে বিলুপ্ত হইত না। বর্ত্তমানে এক চট্টগ্রাম জেলায় কয়েক সহস্র বৌদ্ধ ব্যতীত বাংলা ও বিহারে বৌদ্ধধর্ম্মের চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে।
.
৯. সহজিয়া ধৰ্ম্ম
প্রাচীনকাল হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মমতের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের এই বিবর্ত্তনের ইতিহাস এক্ষেত্রে আলোচনা করা সম্ভব নহে। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, হুয়েন সাং সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত দেখিয়াছিলেন, তাহা গৌতম বুদ্ধ, অশোক, এমনকি কনিষ্কের সময়কার বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষা অনেক পৃথক। কিন্তু পালযুগে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম্ম যে রূপ ধারণ করিয়াছিল, তাঁহার প্রকৃতি ইহা হইতেও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। প্রাচীন সর্ব্বাস্তিবাদ, সম্মিতীয় প্রভৃতি বৌদ্ধ মত তখন বিলুপ্ত হইয়াছে। এমনকি, অপেক্ষাকৃত আধুনিক মহাযান মতবাদও বজ্রযান ও তন্ত্রযান প্রভৃতিতে পরিণত হইয়া সম্পূর্ণ নূতন আকার ধারণ করিয়াছে।
ছোটখাটো প্রভেদ থাকিলেও এই নূতন ধর্ম্মমতগুলির মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য ছিল এবং মোটের উপর ইহাদিগকে সহজযান বা সহজিয়া ধৰ্ম্ম বলা যাইতে পারে। এই ধৰ্ম্মের আচাৰ্য্যগণ সিদ্ধাচাৰ্য নামে খ্যাত। মোট ৮৪ জন সিদ্ধাচাৰ্য্য ছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেই সম্ভবত এই সমুদয় সিদ্ধাচার্যগণ জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা অপভ্রংশ ও দেশীয় ভাষায় গ্রন্থ লিখিতেন। তিব্বতীয় বৌদ্ধ আচাৰ্য্যগণ বাংলা ও বিহারের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের সহায়তায় এই সমুদয় গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় তর্জমা করেন এবং সে তর্জমা তিব্বতীয় তেজুর নামক গ্রন্থে আছে। মূল গ্রন্থগুলি কিন্তু প্রায় সবই বিলুপ্ত হইয়াছে। প্রাচীন বাংলা ভাষায় রচিত যে চর্য্যাপদগুলির কথা পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা এই সিদ্ধাচার্যগণেরই রচিত। এই চর্যাপদ ও সিদ্ধাচাৰ্য্য সরহ ও কৃষ্ণের দোহাকোষ প্রভৃতি যে কয়েকখানি মূল সহজিয়া গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে এই নূতন ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা যাইতে পারে।
এই ধর্ম্মে গুরুর স্থান খুব উচ্চ। “ধৰ্ম্মের সূক্ষ্ম উপদেশ গুরুর মুখ হইতে শুনিতে হইবে, পুস্তক পড়িয়া কিছু হইবে না; গুরু বুদ্ধ অপেক্ষাও বড়; গুরু যাহা বলিবেন বিচার না করিয়া তাহা তৎক্ষণাৎ করিতে হইবে”–ইহাই এই ধৰ্ম্ম সম্প্রদায়ের মূলনীতি।
বৈদিক ধর্ম্ম, পৌরাণিক পূজা-পদ্ধতি, জৈন এবং এমনকি বৌদ্ধধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতি যেরূপ তীব্র শ্লেষ, কটাক্ষ ও ব্যাঙ্গোক্তি এই সমুদয় গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে, তাহা পড়িলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে খৃষ্টীয় মিশনারী কর্ত্তৃক হিন্দুধর্ম্মের সমালোচনার কথা স্মরণ হয়। সরহের দোহাকোষ হইতে দুই একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। “হোম করিলে মুক্তি যত হোক না হোক, ধোঁয়ায় চক্ষের পীড়া হয় এই মাত্র।” “ঈশ্বরপরায়ণেরা গায়ে ছাই মাখে, মাথায় জটা ধরে, প্রদীপ জ্বালিয়ে ঘরে বসিয়া থাকে, ঘরের ঈশান কোণে বসিয়া ঘণ্টা চালে, আসন করিয়া বসে, চক্ষু মিটমিট করে, কানে খুসখুস করে ও লোককে ধাঁধা দেয়।” “ক্ষপণকেরা কপট মায়াজাল বিস্তার করিয়া লোক ঠকাইতেছে; তাহারা তত্ত্ব জানে না, মলিন বেশ ধারণ করিয়া থাকে। এবং আপনার শরীরকে কষ্ট দেয়; নগ্ন হইয়া থাকে এবং আপনার কেশোৎপাটন করে। যদি নগ্ন হইলে মুক্তি হয়, তাহা হইলে শৃগাল কুকুরের মুক্তি আগে হইবে।”
বৌদ্ধ শ্রমণদের সম্বন্ধে উক্তি এইরূপ :
“বড় বড় স্থবির আছেন, কাহারও দশ শিষ্য, কাহারও কোটি শিষ্য, সকলেই গেরুয়া কাপড় পরে, সন্ন্যাসী হয় ও লোক ঠকাইয়া খায়। যাহারা হীনযান (তাহারা যদি শীল রক্ষা করে) তাহাদের না হয় স্বর্গই হউক, মোক্ষ হইতে পারে না। যাহারা মহাযান আশ্রয় করে, তাহাদেরও মোক্ষ হয় না, কারণ তাহারা কেহ কেহ সূত্র ব্যাখ্যা করে, কিন্তু তাহাদের ব্যাখ্যা অদ্ভুত, সে সকল নূতন ব্যাখ্যায় কেবল নরকই হয়।” উপসংহারে বলা হইয়াছে “সহজ পন্থা ভিন্ন পন্থাই নাই। সহজ পন্থা গুরুর মুখে শুনিতে হয়।”
জাতিভেদ সম্বন্ধে সরহ বলেন : “ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার মুখ হইতে হইয়াছিল; যখন হইয়াছিল তখন হইয়াছিল, এখন ত অন্যেও যেরূপে হয়, ব্রাহ্মণও সেইরূপে হয়, তবে আর ব্রাহ্মণত্ব রহিল কী করিয়া? যদি বল সংস্কারে ব্রাহ্মণ হয়, চণ্ডালকে সংস্কার দেও, সে ব্রাহ্মণ হোক; যদি বল বেদ পড়িলে ব্রাহ্মণ হয়, তারাও পড়ক। আর তারা পড়েও ত, ব্যাকরণের মধ্যে ত বেদের শব্দ আছে।”
এইরূপে সিদ্ধাচার্যগণ সমুদয় প্রাচীন সংস্কার ও ধর্ম্মমতের তীব্র সমালোচনা করিয়া যে স্বাধীন চিন্তা ও বিচারবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পড়িলে মনে হয় যে, মধ্যযুগে ও বর্ত্তমানকালে যে সমুদয় প্রাচীন-পন্থা-বিরোধী উদার ধর্ম্মমতবাদ এদেশে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা কেবল ইসলাম বা খৃষ্টীয় ধর্ম্ম এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। যে সংস্কার-বিমুক্ত স্বাধীন চিত্ত ও চিন্তাশক্তির উপর এইগুলি প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার মূল সহজিয়া-মতবাদে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই সহজিয়ামতই আবার চরম গুরুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। একদিকে সূক্ষ্ম স্বাধীন চিন্তা, অপরদিকে নির্বিচারে গুরুর প্রতি আস্থা-এই পরস্পরবিরুদ্ধ মনুষ্য-প্রবৃদ্ধির উপর কিরূপে সহজিয়া ধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। কিন্তু পরবর্ত্তীকালের বাংলার ধর্ম্ম ও সমাজের ইতিহাসে এরূপ বিরুদ্ধ মনোবৃত্তির একত্র সমাবেশ বিরল নহে।
যে ধর্ম্মে কেবলমাত্র গুরুর বচনই প্রামাণিক, তাঁহার সাধন-প্রণালী অনেক পরিমাণেই গুহ্য ও রহস্যে আবৃত। সুতরাং সহজিয়া ধর্ম্মের সাধারণ বিবরণ ব্যতীত বিস্তৃত বিশ্লেষণ সম্ভবপর নহে। এই ধর্ম্মে গুরু প্রথমত সাধকের আধ্যাত্মিক শক্তির উৎকর্ষ অপকর্ষ বিবেচনা করিয়া তাঁহার জন্য তদনুযায়ী সাধন মার্গ নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন। এই শক্তির পরিমাণ অনুসারে পাঁচটি কুল (শ্রেণী) কল্পিত হইয়াছিল-ইহাদের নাম ডোম্বী, নটী, রজকী, চণ্ডালী ও ব্রাহ্মণী। যে পঞ্চ মহাভূত দেহের প্রধান উপকরণ (স্কন্ধ) তাঁহার উপরই এই কুল-বিভাগ প্রতিষ্ঠিত। উপাসকের মধ্যে কোন স্কন্ধটি কিরূপ প্রবল তাহা স্থির করিয়া গুরু তাঁহার প্রজ্ঞা বা শক্তির স্বরূপ নির্ণয় করেন। পরে যে সাধন-প্রণালী অনুসরণ করিলে ঐ বিশেষ শক্তির বৃদ্ধি হইতে পারে প্রতি সাধকের জন্য তিনি তাঁহার ব্যবস্থা করেন।
এই সাধন-প্রণালী এক প্রকার যোগবিশেষ। শরীরের মধ্যে যে ৩২টি নাড়ী আছে তাঁহার মধ্য দিয়ে শক্তিকে মস্তকের সর্বোচ্চ প্রদেশে (মহাসূক্ষ্ম স্থানে) প্রবাহিত করা এই যোগের লক্ষ্য। এই স্থানটি চতুঃষষ্ঠি অথবা সহস্রদল পদ্মরূপে কল্পিত হইয়াছে। রেলওয়ে লাইনে যেমন স্টেশন ও জংশন আছে, দেহাভ্যন্তরের নাড়ীগুলিরও সেই বিরাম ও সংযোগস্থল আছে; ইহাগিদকে পদ্ম ও চক্রের সহিত তুলনা করা হইয়াছে এবং ঊর্ধ্বগমনকালে শক্তিকে এই সমুদয় অতিক্রম করিতে হয়। শক্তি যখন মহাসূক্ষ্মস্থানে পৌঁছে তখন সাধনার শেষ ও সাধকের পরম ও চরম আনন্দ অর্থাৎ মহাসুখ লাভ হয়। সাধকের নিকট তখন বহির্জগৎ লুপ্ত হয়, ইন্দ্রিয়াদি কিছুরই জ্ঞান থাকে না। সাধক, জগৎ, বুদ্ধ সব একাকার হইয়া যায়,-অদ্বৈত জ্ঞান ব্যতীত আর সকলই শূন্যতাপ্রাপ্ত হয়।
সহজিয়া ধর্ম্মের ইহাই মূল তত্ত্ব। তবে বজ্রযান, সহজযান, কালচক্রযান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধন-প্রণালীর মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। বজ্রযানে সাধক সাঙ্কেতিক মন্ত্রোচ্চারণের সাহায্যে দেব-দেবীকে পূজা করেন। ইহার ফলে দেব-দেবীগণ মণ্ডলাকারে সাধকের চতুর্দিকে উপবিষ্ট হন। তখন আর তাঁহার মন্ত্র উচ্চারণ করিবার শক্তি থাকে না, কেবলমাত্র মুদ্রা অর্থাৎ হস্তের ও অঙ্গুলির নানারূপ বিন্যাস দ্বারাই পূজা করিতে হয়। সহজযানে এইসব পূজার বিধি নাই। কালচক্রযানেও উল্লিখিত যোগ সাধনাই প্রধান, এবং এই সাধনার উপযুক্ত কাল, অর্থাৎ মুহূর্ত, তিথি, নক্ষত্রের উপরেই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে।
চরম গুরুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ও গোপন রহস্যে আবৃত থাকায় সহজিয়া ধৰ্ম্ম ক্ৰমেই আধ্যাত্মিক অধঃপতনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। বৌদ্ধধর্ম্মের বিধিবিধান যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া লোপ পাইল। অনুরূপ কারণে হিন্দুর তন্ত্রোক্ত সাধনাও এই অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল। ক্রমে সহজিয়া ধর্ম্ম ও তান্ত্রিক সাধনা একাকার হইয়া বাংলার ধৰ্ম্ম-জগতে যে বীভৎসতার সৃজন করিল তাঁহার বিস্তৃত পরিচয় অনাবশ্যক।
বাংলার শাক্ত ধৰ্ম্মও এই সহজিয়া মতের সহিত মিলিত হইয়া গেল। ফলে একদিকে নূতন নূতন শাক্ত সম্প্রদায় ও অপরদিকে নাথপন্থী, সহজিয়া, অবধূত, বাউল প্রভৃতির সৃষ্টি হইল।
সম্প্রতি নেপালে এই প্রকার এক নূতন শাক্ত সাম্প্রদায়ের কতকগুলি শাস্ত্রগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সম্প্রদায় কৌল নামে অভিহিত এবং ইহার গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ। কৌল নামটি কুল শব্দ হইতে উৎপন্ন, এবং এই কুল বা শ্রেণীবিভাগ যে সহজিয়া ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই কৌল সম্প্রদায়ের লোকেরা কৌল, কুলপুত্র অথবা কুলীন নামে অভিহিত হইয়াছে এবং ইহাদের শাস্ত্রের নাম কুলাগম অথবা কুলশাস্ত্র। কুলই শক্তি: শিব অকুল; এবং দেহাভ্যন্তরে প্রচ্ছন্ন দেবী শক্তির নাম কুলকুণ্ডলিনী। এই ধর্ম্মের আলোচনা করিলে সন্দেহমাত্র থাকে না যে, ইহার প্রধান তত্ত্বগুলি সহজিয়া মতবাদ হইতে গৃহীত। কিন্তু একটি বিষয়ে ইহার প্রভেদ ছিল। ইহা জাতিভেদ মানিয়া চলিত। এই জন্যই ইহা ব্রাহ্মণ্য শাক্ত সম্প্রদায়ের সহিত মিশিতে পারিয়াছিল এবং হিন্দুসমাজে ইহার প্রাধান্য সহজে নষ্ট হয় নাই। যাহারা বর্ণাশ্রম মানিত না, তাহারাই ক্রমে নাথপন্থী, সহজিয়া, অবধূত, বাউল প্রভৃতি বৰ্ত্তমানকালে সুপরিচিত সম্প্রদায়গুলি সৃষ্টি করিয়াছে। এই সকল সম্প্রদায়ের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। তবে ইহারা সকলেই কালক্রমে-হিন্দু যুগের অবসানের পরে-বাংলার ধৰ্ম্মজগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। নাথপন্থীদের গুরু মৎস্যেন্দ্রনাথ ও তাঁহার শিষ্য গোরক্ষনাথের কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ময়নামতীর গান হইতে বুঝা যায় যে এককালে বাংলা দেশে ইহাদের প্রভাব খুব বেশি ছিল। সহজিয়া সম্প্রদায় ও মহাপ্রভু চৈতন্যের পূর্ব্বেই প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল। বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস একজন সহজিয়া ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে সহজিয়া সম্প্রদায় বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হইয়া, পরম সত্যকে কৃষ্ণ ও তাঁহার শক্তিকে রাধারূপে কল্পনা করে; কিন্তু নাড়ী, চক্র প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম্মের যোগসাধন-প্রণালী একেবারে পরিত্যাগ করে নাই। চণ্ডীদাসের রজকিনী প্রেম প্রাচীন সহজিয়া ধর্ম্মের পঞ্চকুলের অন্যতম রজকীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বাউল সম্প্রদায় বৈষ্ণব প্রভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া প্রাচীন বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্ম্মের সহিত ঘনিষ্ঠ রক্ষা যোগসূত্র রক্ষা করিতে পারিয়াছে।
বাংলায় বৌদ্ধধর্ম্মের যে রূপান্তর ঘটিয়াছিল, তাঁহার অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা করা হইল,-কারণ যত দূর জানা যায় তাহাতে ইহাই ধৰ্ম্মজগতে বাংলার বিশিষ্ট দান বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। অন্য যে সমুদয় ধর্ম্মমত বাংলায় প্রচলিত ছিল-তাহা মোটামুটিভাবে নিখিল ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মেরই অনুরূপ, তাঁহার মধ্যে বাংলার বৈশিষ্ট্য কিছু থাকিলেও তাহা নিরূপণ করিবার কোনো উপায় নাই। কিন্তু অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের যে রূপান্তর ঘটিয়াছিল তাঁহার উপর ব্লাঙ্গালীর প্রভাবই যে বেশী একথা সকলেই স্বীকার করেন। এই রূপান্তরই আবার বাংলার অন্যান্য ধর্ম্মমতের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া বাংলার ধর্ম্ম ও সমাজে যে বিপ্লব ঘটাইয়াছিল, বাংলার মধ্যযুগে, এমনকি বর্ত্তমানকালেও তাঁহার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বৌদ্ধধর্ম্ম বাংলা হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে-একথা এক হিসাবে সত্য। কিন্তু এত বড় একটা ধর্ম্মমত যে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে ধর্ম্মঠাকুরের পূজাই বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ। কিন্তু বাংলার বৌদ্ধধর্ম্ম কেবলমাত্র এই সব লৌকিক অনুষ্ঠানেই পৰ্য্যবসিত হয় নাই। উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে যে, যে সমুদয় ধর্ম্মমত মধ্যযুগে বাংলায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল তাহা অনেকাংশে প্রত্যক্ষ অথবা প্রচ্ছন্নভাবে বৌদ্ধমতের পরিণতি মাত্র।
.
১০. বাংলার ধর্ম্মমত
এ পর্য্যন্ত আমরা বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে পৃথকভাবে আলোচনা করিয়াছি। উপসংহারে বাংলার ধর্ম্মমত সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ তথ্যের উল্লেখ আবশ্যক। প্রাচীন বাংলায় বৈদিক, পৌরাণিক, বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মের আপেক্ষিক প্রভাব ও প্রতিপত্তি কিরূপ ছিল তাহা জানিতে স্বতই ইচ্ছা হয়। পূৰ্ব্বে হুয়েন সাংয়ের যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ ও জৈনদিগের তুলনায় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা খুব বেশী ছিল। ঐ সময়ে জৈনগণের সংখ্যাও অনেক ছিল। পরবর্ত্তীকালে জৈনগণের সংখ্যা খুবই কমিয়া যায়, কিন্তু পৌরাণিক ধৰ্ম্ম পূৰ্ব্ববৎ বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী ছিল কি না, ইহা নিশ্চিত বলা যায় না। পালরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম্ম যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করিলেও ইহার প্রভাব যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছিল, অনেকে এরূপ মনে করেন না। কারণ অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর যে সমুদয় মূর্ত্তি বা লিপি এযাবৎ পাওয়া গিয়াছে, তাঁহার অধিকাংশই পৌরাণিক ধর্ম্মের প্রভাব সূচিত করে। তবে ইহা অসম্ভব নহে যে, বৌদ্ধধৰ্ম্ম জনসাধারণের মধ্যে বেশি প্রচলিত ছিল এবং পৌরাণিক ধৰ্ম্ম সাধারণত ধনী, শিক্ষিত ও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সহজিয়া ধর্ম্মের বিবরণ হইতে এরূপ ধারণা করা অসঙ্গত হইবে না যে, সমাজের নিম্নস্তরের মধ্যেই ইহার বিশেষ প্রসার ছিল। ডোম্বী, নটী, রজকী, চণ্ডালী প্রভৃতি কুলের নামে ইহার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় এবং চর্য্যাপদগুলি পাঠ করিলেও এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়। পরবর্ত্তীকালে সহজিয়া বৌদ্ধমত হইতে যে সমুদয় ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহাও সমাজের নিম্নশ্রেণীর মধ্যেই বেশী প্রচলিত ছিল। সরহের দোহা হইতে জানা যায় যে, সিদ্ধাচার্যগণ ব্রাহ্মণের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে তীব্র মত পোষণ করিতেন, এবং স্বীয় সম্প্রদায়ে জাতিভেদ প্রথা দূর করিয়াছিলেন। অসম্ভব নহে যে, সহজিয়া মতের জনপ্রিয়তার ইহাও একটি কারণ। বাংলা দেশে মোট জনসংখ্যার তুলনায় উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ সংখ্যায় এত কম কেন, এই সমস্যার কোনো সন্তোষজনক মীমাংসা হয় নাই। বাংলায় হিন্দু যুগের শেষে বৌদ্ধমতের প্রভাব ইহার অন্যতম কারণ বলিয়া অনুমান করা খুব অসঙ্গত নহে।
শৈব ও বৈষ্ণব এই দুই ধৰ্ম্মমতের মধ্যে কোনটি প্রবল ছিল, তাহা বলা শক্ত। তবে হিন্দু যুগের শেষ দুই-তিন শতাব্দীর যে সমুদয় মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাঁহার সংখ্যামূলক তুলনা করিলে বৈষ্ণব ধর্ম্মমতেরই প্রাধান্য সূচিত হয়।
রাজগণের ধর্ম্মমত অনেক সময় অন্তত কতক পরিমাণে জনসাধারণের ধর্ম্মমত প্রতিফলিত করে। সুতরাং বাংলার রাজগণের ধর্ম্মমত কিরূপ ছিল, তাঁহার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি অধ্যায়ে বিভিন্ন রাজবংশের যে ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, খড়গ, চন্দ্র ও পালবংশ এবং কান্তিদেব, রণবঙ্কমল্ল প্রভৃতি রাজা বৌদ্ধ ছিলেন। বৈন্যগুপ্ত শশাঙ্ক, লোকনাথ, ডোম্মনপাল এবং সেনবংশীয় বিজয়সেন ও বল্লালসেন শৈব ছিলেন। বর্ম্মণ ও দেববংশ এবং বল্লালসেনের পরবর্ত্তী সেনবংশীয় রাজগণ বৈষ্ণব ছিলেন। গুপ্তযুগের পরবর্ত্তী বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজগণ-গোপচন্দ্ৰ ধৰ্ম্মাদিত্য, সমাচারদেব-ব্রাহ্মণ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা শৈব, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন কি না, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।
এই সমুদয় বিভিন্ন সম্প্রদায় বর্ত্তমান থাকিলেও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বাংলায়ও যে ইহাদের মধ্যে কলহ ও দ্বেষ হিংসা ছিল না, বরং যথেষ্ট সম্ভাব ছিল, তাঁহার বহু প্রমাণ আছে। রাজগণ ধর্ম্ম বিষয়ে উদার মত পোষণ করিতেন। বৌদ্ধ পালরাজগণ যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম বিষয়ে বিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তাঁহাদের শাসনলিপি হইতেই তাহা প্রমাণিত হয়। ধর্ম্মপাল ও তৃতীয় বিগ্রহপাল যে বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্ম মানিয়া চলিতেন, দুইখানি তাম্রশাসনে তাঁহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। নারায়ণপাল নিজে একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া অনেকবার শ্রদ্ধা-সলিলাপুত-হৃদয়ে নতশিরে, পবিত্র (শান্তি) বারি গ্রহণ করিয়াছিলেন”। মদনপালের প্রধানা মহিষী চিত্রমতিকা মহাভারত-পাঠ শ্রবণ করিয়া দক্ষিণস্বরূপ ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ দেবখগের মহিষী প্রভাবতী চণ্ডীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অপরদিকে শৈব রাজা বৈন্যগুপ্ত বৌদ্ধবিহার নির্মাণ, এবং একজন ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক সোমপুরের জৈন বিহারের ব্যয় নিৰ্বাহাৰ্থ ভূমিদান করিয়াছিলেন। রাজা শ্রীধরণরাতের মন্ত্রী জয়নাথ বৌদ্ধবিহার ও ব্রাহ্মণদিগকে ভূমিদান করেন। এই সমুদয় দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, সেকালে পরস্পরের ধর্ম্মমতের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। কান্তিদেবের তাম্রশাসনে ইহার আরও ব্যাপক পরিচয় পাই। তাঁহার পিতা ধনদও বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মাতা ছিলেন শিবের উপাসিকা। ধনদত্ত বৌদ্ধ হইলেও রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ প্রভৃতিতে অভিজ্ঞ ছিলেন, একথা তাঁহার পুত্রের তাম্রশাসনে স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে।
তৎকালে শৈব, বৈষ্ণব, সৌর প্রভৃতি পৌরাণিক বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে কেবলমাত্র যে সদ্ভাব ছিল তাহা নহে, ইহাদের ব্যবধানরেখাও সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট হইয়া ওঠে নাই। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে তাঁহাকে পরম-মাহেশ্বর ডোম্মনপালের তাম্রশাসনে ভগবান নারায়ণের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেনের সদাশিব মুদ্রা-সংযুক্ত তাম্রশাসনে প্রথমে নারায়ণ ও পরে সূর্য্যের স্তব আছে, কিন্তু উক্ত রাজগণ পরমসৌর বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এই তাম্রশাসনগুলি শৈব, বৈষ্ণব ও সৌর সম্প্রদায়ের অপূৰ্ব্ব সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত।
.
দ্বিতীয় খণ্ড –দেব-দেবীর মূর্ত্তি পরিচয়
বাংলা দেশের প্রায় সৰ্ব্বত্রই বহু দেব-দেবীর মূর্ত্তি, আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের উল্লেখ বা বিস্তৃত বর্ণনা করা বর্ত্তমান গ্রন্থে সম্ভবপর নহে। সুতরাং সংক্ষেপেই এ বিষয়টি আলোচনা করিব।
১. বিষ্ণমূৰ্ত্তি
বিষ্ণুমূৰ্ত্তির চারিহস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম থাকে। কোনো কোনো স্থলে চক্র ও গদার প্রতিকৃতির পরিবর্তে একটি পুরুষ ও নারীমূর্ত্তি দেখা যায়। ইহাদের নাম চক্ৰপুরুষ ও গদাদেবী। বিষ্ণুর ভিন্ন ভিন্ন হস্তে এই চারিটি ভূষণ পরিবর্ত্তন করিয়া ২৪টি বিভিন্ন প্রকারের বিষ্ণুমূর্ত্তি পরিকল্পিত হইয়াছে। বাংলায় সচরাচর ত্রিবিক্রম রূপের বিষ্ণুই দেখা যায়। ইহার নিম্ন ও উৰ্দ্ধবাম এবং উৰ্দ্ধ ও নিম্নদক্ষিণ হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম, এবং দুই পার্শ্বে শ্রী ও পুষ্টি অর্থাৎ লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মূর্ত্তি। মালদহ জিলার হাঁকরাইল গ্রামে প্রাপ্ত মূর্ত্তিই সম্ভবত বাঙ্গালার সৰ্ব্বপ্রাচীন বিষ্ণুমূৰ্ত্তি। ইহার পদদ্বয় ও দুই হস্ত ভগ্ন এবং নিম্নদক্ষিণ হস্তে পদ্ম ও উপরের বাম হস্তে শঙ্খ। মূর্ত্তিটির মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, গলায় হার, বাহুতে অঙ্গদ ও বক্ষোদেশে যজ্ঞোপবীত।
বরিশাল জিলার অন্তর্গত লক্ষ্মণকাটি গ্রামে একটি প্রকাণ্ড বিষ্ণুমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহার উচ্চতা ৬’-৪”। ঊর্ধ্বে উড্ডীয়মান ত্রিনেত্র গরুড়ের পক্ষোপরি বিষ্ণু ললিতাসনে উপবিষ্ট। তাঁহার উৰ্দ্ধদক্ষিণ ও বাম হস্তে ধৃত পদ্মনালের উপর যথাক্রমে লক্ষ্মী (গজ লক্ষ্মী) ও বীণাবাদিনী বাণীমূর্ত্তি। অন্য দুই হস্তে চক্ৰপুরুষসহ চক্র ও গদাদেবী। মস্তকের ষট্কোণ কিরীটের মধ্যস্থলে ধ্যানস্থ চতুর্ভুজ দেবমূর্ত্তি। হস্তোপরি লক্ষ্মী ও সরস্বতী (শ্ৰী ও পুষ্টি) এবং কিরীটস্থ ধ্যানী দেবমূৰ্ত্তি,-এই দুইটিই আলোচ্য মূর্ত্তির বিশেষত্ব, এবং ইহা সম্ভবত বৌদ্ধ মহাযান মতের প্রভাব সূচিত করে। কেহ কেহ এই মূর্ত্তিটি গুপ্তযুগের বলিয়া মনে করেন, কিন্তু ইহা সম্ভবত আরও অনেক পরবর্ত্তী কালের।
চৈতন্যপুরের (বর্দ্ধমান) একটি বিষ্ণুমূৰ্ত্তির পরিকল্পনায়ও বিশেষত্ব আছে। গদা ও চক্রের নীচে গদাদেবী ও চক্ৰপুরুষ। দণ্ডায়মান বিষ্ণুর দুই হস্ত ঘঁহাদের মাথায় আর দুই হস্তে শঙ্খ ও পদ্ম। মূর্ত্তিটির মুখাকৃতি ও পরিহিত বসন সবই একটু অদ্ভুত রকমের। ইহা সম্ভবত বৈখানসাগমে বর্ণিত অভিচারক-স্থানক মূর্ত্তি।
সাগরদীঘিতে প্রাপ্ত অষ্টধাতুনির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তির বিশেষত্ব এই যে তাঁহার তিনটি ভূষণ-শঙ্খ, চক্র ও গদা-একটি পূর্ণ-প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর রক্ষিত এবং প্রতি পদ্মের নালটি বিষ্ণু হস্তে ধরিয়া আছেন।
দিনাজপুর জিলার সুরাহর গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূৰ্ত্তি সাতটি নাগফণার নীচে দণ্ডায়মান। শ্রী ও পুষ্টির পরিবর্তে দুইপার্শ্বে দুইটি পুরুষমূর্ত্তি (সম্ভবত শঙ্খপুরুষ ও চক্ৰপুরুষ)। মধ্যস্থিত নাগফণার উপরিভাগে ক্ষুদ্র দ্বিভুজ ধ্যানী মূর্ত্তি এবং পাদপীঠের মধ্যভাগে ষড়ভুজ নৃত্যপরায়ণ শিব। অনেকে অনুমান করেন যে, উপরিস্থিত ধ্যানীমূৰ্ত্তি ব্রহ্মা এবং সমগ্র মূর্ত্তিটি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব এই ত্রিমূর্ত্তির পরিকল্পনা। কিন্তু ব্রহ্মার দুই ভুজ ও এক মুখ বড় দেখা যায় না। সুতরাং এ মূর্ত্তিটিও সম্ভবত মহাযান মতের প্রভাবের ফল।
এইরূপ বিশেষত্ব খুব কম মূর্ত্তিতেই দেখা যায়। সচরাচর যে সমুদয় বিষ্ণুমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, বাঘাউরা গ্রামে প্রাপ্ত সম্রাট মহীপালের তৃতীয় রাজ্য সম্বৎসরে উৎকীর্ণ লিপি-সংযুক্ত মূর্ত্তিটি তাঁহার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন (চিত্র নং ১৮)। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী দণ্ডায়মান বিষ্ণুমূৰ্ত্তি উত্তম বসন-ভূষণে সজ্জিত; কিরীট, কুণ্ডল, অঙ্গদ, বনমালা, মেখলা, বসন প্রভৃতি বিচিত্র কারুকাৰ্য্য-খচিত; ঊর্ধে মস্তকোপরি প্রভাবলী, তাঁহার দুই পার্শ্বে পুস্পমাল্য-হস্তে উডড্ডীয়মান বিদ্যাধরযুগলের মূর্ত্তি, মূর্ত্তির পশ্চাতে সিংহাসন ও অধোদেশে দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী; পাদপীঠের মধ্যস্থলে প্রস্ফুটিত পদ্মদলের উপর বিষ্ণুর চরণযুগল; ইহার দক্ষিণভাগে দুইটি ও বামভাগে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি, সম্ভবত ইহারা মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠাকারী ও তাঁহার পরিবারবর্গ।
বিষ্ণুমূৰ্ত্তি সাধারণত দণ্ডায়মান (চিত্র নং ১৯), কিন্তু কোনো কোনো স্থলে অর্দ্ধশয়ান, অথবা যোগাসনে উপবিষ্ট। কোনো কোনো মূর্ত্তিতে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী একত্র উপবিষ্ট দেখা যায়। ঢাকা জিলাস্থিত বাস্তা গ্রামের লক্ষ্মী-নারায়ণ মূৰ্ত্তি ইহার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বিষ্ণু ও তাঁহার বাম উরুর উপর লক্ষ্মী, এই যুগলমূৰ্ত্তি গরুড়ের পৃষ্ঠদেশে বসিয়া আছেন। উভয়েরই একটি চরণ গরুড়ের প্রসারিত এক এক হস্তে র উপর স্থাপিত। গরুড়ের অন্য দুইটি হস্ত সম্মুখে অঞ্জলিবদ্ধ।
বিষ্ণুর দশ অবতারের মূর্ত্তি-সম্বলিত প্রস্তরখণ্ড অনেক পাওয়া গিয়াছে। পৃথকভাবে বরাহ, নরসিংহ ও বামন অবতারের মূর্ত্তিই সাধারণত দেখা যায়। মৎস্য, বলরাম ও পরশুরাম এই তিন অবতারেরও মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মৎস্য মূর্ত্তি চতুর্ভুজ; ঊর্ধ্বদেশ মানুষের ও অধোদেশ মৎস্যের আকৃতি (চিত্র নং ২০)। বরাহমূৰ্ত্তিরও কেবল মুখটি বরাহের, অন্যান্য অংশ মানুষের মতন।
রাজসাহী চিত্রশালায় একটি দণ্ডায়মান মূৰ্ত্তির বিশ হস্তে গদা, অঙ্কুশ, খড়গ, মুদ্র, শূল, শর, চক্র, খেটক, ধনু, পাশ, শঙ্খ প্রভৃতি আয়ুধ। দুই পার্শ্বে স্থুলোদর দুইটি মূর্ত্তি। মূল মূৰ্ত্তি বনমালা ও অন্যান্য ভূষণে ভূষিত। ইহা সম্ভবত বিষ্ণুর বিশ্বরূপ মূর্ত্তি।
ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর একাত্মক একটি মূৰ্ত্তি উত্তরবঙ্গে পাওয়া গিয়াছে। চতুর্মুখ ব্রহ্মার তিনটি মুখই কেবল দেখা যায়; তাঁহার চারি হস্তে সুক, সুব, অক্ষমালা ও কমণ্ডলু। মূৰ্ত্তির দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী, সরস্বতী, শঙ্খপুরুষ ও চক্ৰপুরুষ এবং গলে বনমালা বিষ্ণুর নিদর্শন। পাদপীঠের এক পার্শ্বে ব্রহ্মার বাহন হংস ও অপর পার্শ্বে বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের মূর্ত্তি।
ব্রহ্মার যে সমুদয় পৃথক মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহাও চতুর্মুখ (একটি অদৃশ্যমান) ও স্থূলোদর এবং তাঁহার বাহন ও চারি হস্তে ধৃত দ্রব্যাদি উক্ত মূর্ত্তির অনুরূপ।
সাধারণত বিষ্ণুমূর্ত্তির বাহন ও পার্শ্বচরীরূপে পরিকল্পিত হইলেও গরুড়, (চিত্র নং ২৭ গ) লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পৃথক মূৰ্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। রাজসাহী চিত্রশালায় এইরূপ একটি গরুড়মূৰ্ত্তি রক্ষিত আছে। ইহার অঞ্জলিবদ্ধ হস্তে ও মুখশ্রীতে সেবকের ভক্তি ও শ্রদ্ধার ভাব চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে।
বগুড়ায় একটি চমৎকার অষ্টধাতুনির্ম্মিত লক্ষ্মীমূৰ্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান দেবীর তিন হস্তে ফল, অঙ্কুশ ও ঝাঁপি (আর এক হস্ত ভগ্ন); দুই পার্শ্বে চামরহস্তে পার্শ্বচরী; মস্তকোপরি প্রস্ফুটিত পদ্মদলের দুই দিক হইতে দুইটি হস্তী শুণ্ডধৃত কলসীর জল দিয়া দেবীকে স্নান করাইতেছে। লক্ষ্মীর এই প্রকার গজমূৰ্ত্তিই সাধারণত দেখা যায়। কিন্তু দুই হস্তবিশিষ্ট সাধারণ লক্ষ্মীমূৰ্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে।
সরস্বতীর মূর্ত্তি সাধারণত চারি হস্ত-বিশিষ্ট। দেবী দুই হস্তে বীণা বাজাইতেছেন, অপর দুই হস্তে অক্ষমালা ও পুস্তক। দেবীর দুই পার্শ্বে চামরধারিণী, পাদপীঠে কোনো কোনো স্থলে তাঁহার সুপরিচিত বাহন হংস, কিন্তু কোনো স্থলে আবার একটি মেষের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ছাতিনা গ্রামে প্রাপ্ত সরস্বতীর মূর্ত্তি (চিত্র নং ২৩) ইহার চমৎকার দৃষ্টান্ত।
.
২. শৈবমূর্ত্তি
শিব সাধারণত লিঙ্গরূপেই পূজিত হইতেন। লিঙ্গ প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। সাধারণ শিবলিঙ্গ বাংলায় সুপরিচিত এবং চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্ত্তির ন্যায় ইহাও এদেশে বহু সংখ্যায় পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু আর এক প্রকার লিঙ্গ আছে। ইহাতে লিঙ্গের উপর শিবের মুখ খোদিত থাকে, ইহার নাম মুখলিঙ্গ। মুখের সংখ্যা অনুসারে মুখলিঙ্গ একমুখ বা চতুর্মুখ। একমুখ লিঙ্গই বেশী পাওয়া যায়। ত্রিপুরা জিলায় উনকোটি গ্রামে প্রস্তরনির্ম্মিত এবং মুর্শিদাবাদে অষ্টধাতুর চতুর্মুখ লিঙ্গ পাওয়া গিয়াছে।
শিবের মূর্ত্তি নানারূপে কল্পিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে চন্দ্রশেখর, নটরাজ বা নৃত্যমূৰ্ত্তি, সদাশিব, উমা-মহেশ্বর, অর্দ্ধনারীশ্বর ও কল্যাণ-সুন্দর, শিবের সৌম্য ভাব দ্যোতক, এবং অঘোর-রুদ্র তাঁহার উগ্রভাবের পরিকল্পনা। পাহাড়পুরে শিবের তিনটি চন্দ্রশেখর-মূৰ্ত্তি খোদিত আছে। ইহাদের তিন নেত্র, উলিঙ্গ ও জটামুকুট এবং দুই হস্তে ত্রিশূল, অক্ষমালা ও কমণ্ডলু প্রভৃতি লক্ষিত হয়। একটি মূর্ত্তিতে সর্প শিবের গলদেশে জড়াইয়া আছে। বিবসন হইলেও শিবের গলায় হার, কর্ণে, কুণ্ডল এবং বাহুতে কেয়ুর প্রভৃতি ভূষণ ও গলায় যজ্ঞোপবীত আছে।
পরবর্ত্তীকালে শিবের মূর্ত্তিতে আরও অনেক বৈচিত্র্য ও উপাদান-বাহুল্য দেখা যায়। রাজসাহী জিলার গণেশপুরে প্রাপ্ত মূৰ্ত্তি (চিত্র নং ২২ ক) ইহার এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। চতুর্ভুজ মূর্ত্তির এক হস্তে দীর্ঘ দলবিশিষ্ট পদ্ম, আর এক হস্তে শূল অথবা খট্টাঙ্গ (অপর দুই হস্ত ভগ্ন)। বিচিত্র কারুকাৰ্য্যশোভিত সপ্তরথ পাদপীঠের কেন্দ্রস্থলে বিশ্বপদ্মের উপর নানা বিভূষণে সজ্জিত শিব ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান। মস্তকের চতুর্দিকে বিচিত্র প্রভাবলী,ইহার দুই পার্শ্বে মালা হস্তে উড্ডীয়মান গন্ধৰ্ব্ব। মূর্ত্তির পশ্চাতে কারুকার্যখচিত সিংহাসন ও নিম্নে দুই পার্শ্বে দুইজন কিঙ্কর ও কিঙ্করী। কিঙ্করগণের হস্তে শূল ও কপাল এবং কিঙ্করীগণের হস্তে চামর। ইহা শিবের ঈশানমূৰ্ত্তি। বরিশাল জিলার অন্তর্গত কাশীপুর গ্রামে বিরূপাক্ষরূপে পূজিত চতুর্ভুজ শিব সম্ভবত নীলকণ্ঠ। সারদাতিলক তন্ত্র অনুসারে নীলকণ্ঠের পাঁচটি মুখ। এই মূর্ত্তির মুখ মাত্র একটি, কিন্তু উক্ত তন্ত্রের বর্ণনা অনুযায়ী ইহার হস্তে অক্ষমালা, ত্রিশূল, খট্টাঙ্গ ও কপাল আছে। বর্ণনার অতিরিক্ত এই মূর্ত্তিতে কীর্তিমুখের পরিবর্তে ছত্র, প্রভাবলীর দুই পার্শ্বে কার্তিক-গণেশের মূৰ্ত্তি ও নিয়ে দুই পার্শ্বে মকরবাহিনী গঙ্গা ও সিংহবাহিনী পার্ব্বতীর মূর্ত্তি প্রভৃতি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়। মূৰ্ত্তির অধোভাগে শিবের বাহন নন্দীর মূর্ত্তি। বরিশাল জিলায় প্রাপ্ত একটি ব্রঞ্জের শিবমূৰ্ত্তির (চিত্র নং ২৮ খ) শীর্ষদেশে ধ্যানীবুদ্ধের মূর্ত্তির ন্যায় একটি মূর্ত্তি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। এরূপ দ্বিতীয় মূৰ্ত্তি এখনো পাওয়া যায় নাই।
বাংলায় নটরাজ শিবের যে সমুদয় মূৰ্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাঁহার হস্তসংখ্যা দশ অথবা বারো এবং শিব বৃষপৃষ্ঠে নৃত্যপরায়ণ। দক্ষিণ ভারতের নটরাজ বৃষারূঢ় নহেন এবং তাঁহার মাত্র চারি হাত। বাংলার দশভুজ নটরাজ মূর্ত্তির সহিত মৎস্যপুরাণের বর্ণনার ঐক্য আছে। এই বর্ণনা অনুযায়ী শিবের দক্ষিণ চারি হস্তে খড়গ, শক্তি, দণ্ড, ত্রিশূল এবং বাম চারি হস্তে খেটক, কপাল, নাগ ও খট্টাঙ্গ; নবম হস্তে অক্ষমালা, এবং দশম হস্ত বরদামুদ্রাযুক্ত। দ্বাদশভুজ শিবের মূর্ত্তি অন্যরূপ। শিব দুই হস্তে বীণা বাজাইতেছেন, দুই হস্তে তাল দিতেছেন ও আর দুই হস্তে ছত্রের ন্যায় সর্প ধরিয়া আছেন; বাকী হস্তগুলিতে শিবের সুপরিচিত আয়ুধাদি আছে। ঢাকা জিলাস্থিত শঙ্করবাঁধা গ্রামে প্রাপ্ত একটি মূর্ত্তি (চিত্র নং ২২ গ) নটরাজ শিবের সুন্দর দৃষ্টান্ত। ইহার দশ হস্তে মৎস্যপুরাণোক্ত আয়ুধাদি আছে। শিবের বাহন বৃষটিও নৃত্যশীল প্রভুর দিকে মুখ ফিরাইয়া দুই পা ঊর্ধ্বে তুলিয়া নৃত্য করিতেছে। ইহার দুই পার্শ্বে মকরবাহিনী গঙ্গা ও সিংহবাহিনী পার্ব্বতী। মূর্ত্তির উপরে ও উভয় পার্শ্বে প্রধান প্রধান দেব-দেবীর মূর্ত্তি। পাদপীঠে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য নাগ-নাগিনী ও গণের নৃত্যপরায়ণ মূর্ত্তি। শিল্পী পারিপার্শ্বিকের সাহায্যে নটরাজ শিবের সৌন্দর্য্য উজ্জ্বলরূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।
সদাশিব-মূর্ত্তি বাংলায় অনেক পাওয়া গিয়াছে। সেনরাজগণের তাম্রশাসন মুদ্রায় যে এই মূর্ত্তি উল্কীর্ণ তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মহানিৰ্বাণতন্ত্র, উত্তরকামিকাগম এবং গরুড়পুরাণে সদাশিব মূৰ্ত্তির বর্ণনা আছে। শেষোক্ত দুইখানি গ্রন্থের বর্ণনার সহিত বাংলার সদাশিব-মূৰ্ত্তির অধিকতর সঙ্গতি দেখা যায়। এই বর্ণনা অনুসারে বদ্ধপদ্মাসনস্থিত সদাশিব-মূর্ত্তির পাঁচটি মুখ ও দশটি হস্ত থাকিবে। দক্ষিণ দুই হস্ত অভয় ও বরদ মুদ্রাযুক্ত এবং অবশিষ্ট তিন হস্তে শক্তি, ত্রিশূল ও খট্টাঙ্গ; বাম পাঁচ হস্তে সর্প, অক্ষমালা, ডমরু, নীলোৎপল ও লেবুফল থাকিবে। তাঁহার পার্শ্বে মনোম্মানীর মূর্ত্তি থাকিবে। দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত রাজিবপুরে তৃতীয় গোপালের লিপিযুক্ত সদাশিব-মূর্ত্তি বাংলার এই জাতীয় মূর্ত্তির একটি সুন্দর নিদর্শন। ইহাতে মনোম্মানীর মূৰ্ত্তি নাই, কিন্তু পঞ্চরথ পাদপীঠের মধ্যস্থলে শূলধারী দুইটি শিবকিঙ্করের মূর্ত্তি আছে। বাংলার সদাশিব মূর্ত্তিগুলির সহিত দক্ষিণ ভারতে রচিত শাস্ত্রের বর্ণনার সামঞ্জস্য এবং সেনরাজগণের শাসনমুদ্রায় সদাশিব মূর্ত্তি দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সেনরাজগণই দাক্ষিণাত্য হইতে বাংলায় সদাশিব-মূর্ত্তির প্রচলন করেন। কিন্তু যে শৈব আগম হইতে সদাশিব পূজার উৎপত্তি, তাহা উত্তর ভারতেই রচিত হয়। সম্ভবত এই আগমোক্ত সদাশিব পূজা প্রথমে উত্তর ভারত হইতে দাক্ষিণাত্যে প্রচারিত হয়, পরে সেনরাজগণ তথা হইতে ইহা বাংলায় প্রচলন করেন।
শিবের আলিঙ্গন অথবা উমা-মহেশ্বর মূর্ত্তি বাংলায় সুপরিচিত। শিবের বাম জানুর উপর উপবিষ্ট উমা দক্ষিণ হস্তে শিবের গলদেশ বেষ্টন করিয়াছেন এবং বাম হস্তে একখানি দর্পণ ধরিয়া আছেন। শিবের দক্ষিণ হস্তে একটি পদ্ম এবং বাম হস্ত দ্বারা তিনি দেবীকে আলিঙ্গন করিয়া আছেন। সম্ভবত তান্ত্রিক ধৰ্ম্মমতের প্রভাবেই বাংলায় এই মূর্ত্তির বহুল প্রচার হইয়াছিল। কারণ তন্ত্রমতে সাধকগণকে শিবের ক্রোড়ে উপবিষ্টা দেবীমূর্ত্তিকে ধ্যান করিতে হয়, এবং এই প্রকার মূৰ্ত্তি সম্মুখে রাখিলে এই ধ্যানযোগের সুবিধা হয়।
বৈবাহিক অথবা কল্যাণসুন্দর মূর্ত্তিতে শিবের ঠিক সম্মুখেই গৌরী দাঁড়াইয়া আছেন। শেষোক্ত দুই প্রকার মূর্ত্তিতে শিব ও উমার মূর্ত্তি একত্র হইলেও পৃথক। কিন্তু অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিতে উভয়ে এক দেহে পরিণত হইয়াছেন। এই মূর্ত্তির দক্ষিণ-অর্দ্ধ শিবের ও বাম-অৰ্দ্ধ উমার। অর্দ্ধনারীশ্বর ও কল্যাণসুন্দর মূর্ত্তি বাংলায় খুব বেশী পাওয়া যায় নাই।
এ পর্য্যন্ত শিবের যে সমুদয় মূর্ত্তি আলোচিত হইয়াছে, তাহা সৌমাভাবের দ্যোতক। শিবের রুদ্র মূর্ত্তি ভারতের অন্যান্য প্রদেশে খুব প্রচলিত থাকিলেও বাংলায় মাত্র অল্প কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে। এইগুলিতে শিবের দিগম্বর, নরমুণ্ডমালা-বিভূষিত, উলঙ্গ নরদেহের উপর দণ্ডায়মান মূর্ত্তি এবং গুর্ধ-শকুনী পরিবেষ্টিত নরমুণ্ড-রচিত পাদপীঠ প্রভৃতি বীভৎস ভাবের পরিকল্পনা দেখা যায়।
শিবের পুত্র গণেশের বহুসংখ্যক মূর্ত্তি বাংলায় পাওয়া গিয়াছে। উপবিষ্ট, দণ্ডায়মান ও নৃত্যশীল, গণেশের এই তিন প্রকার মূর্ত্তি পরিকল্পিত হইয়াছে। কার্তিকের পৃথক মূৰ্ত্তি খুবই কম। কিন্তু উত্তরবঙ্গে ময়ূরবাহন কার্তিকের একটি সুন্দর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে (চিত্র নং–২১ ক)।
.
৩. শক্তি-মূর্ত্তি
বাংলায় বহুসংখ্যক ও বিভিন্ন শ্রেণীর দেবীমূৰ্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহার কোনো কোনোটিতে বৈষ্ণব প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অধিকাংশই শাক্তগণের আরাধ্য দেবী।
ত্রিপুরা জেলার দেউবাড়ী স্থানে প্রাপ্ত অষ্টধাতুনির্ম্মিত দেবীমূর্ত্তির পাদপীঠে খড়গবংশীয়া রাণী প্রভাবতীর লিপি উৎকীর্ণ আছে। সুতরাং ইহা সপ্তম শতাব্দীর এবং এই শ্রেণীর মূর্ত্তির সর্বপ্রাচীন নিদর্শন। দেবী অষ্টভুজা ও সিংহবাহিনী, এবং তাঁহার হস্তে শঙ্খ, তীর, অসি, চক্র, ঢাল, ত্রিশূল, ঘণ্টা ও ধনু। পরবর্ত্তীকালে রচিত শারদাতিলক-তন্ত্রে এই দেবী দ্রদুর্গা, ভদ্রকালী, অম্বিকা, ক্ষেমঙ্করী ও বেদগর্ভা প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছেন, কিন্তু উত্তীর্ণ লিপি অনুসারে ইহার নাম সৰ্ব্বাণী।
বাংলায় এক শ্রেণীর চতুর্ভুজা দেবীমূৰ্ত্তি সচরাচর দেখা যায়। কেহ কেহ ইহাকে চণ্ডী এবং কেহ কেহ গৌরী-পাৰ্বতী নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই দণ্ডায়মানা দেবীমূৰ্ত্তির হস্তে অক্ষসহ শিবলিঙ্গ, ত্রিদী অথবা ত্রিশূল, দাড়িম্ব ও কমণ্ডলু এবং পাদপীঠে একটি গোধিকার মূর্ত্তি। কোনো কোনো মূৰ্ত্তিতে দেবীর দুই পার্শ্বে কার্তিক-গণেশ অথবা লক্ষ্মী-সরস্বতী, সিংহ, মৃগ, ও কদলী বৃক্ষ, ঊর্ধ্বে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং নবগ্রহ প্রভৃতির মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।
উপবিষ্টা দুর্গামূৰ্ত্তিও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কোনোটি চতুর্ভুজা, কোনোটি ষড়ভুজা। বিংশভুজা একটি মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে–ইনি সম্ভবত মহালক্ষ্মী। বিক্রমপুরের কাগজিপাড়ায় পাষাণ লিঙ্গের উদ্ধৃভাগ হইতে আবির্ভূত একটি দেবীমূৰ্ত্তি পাওয়া গিয়াছে; ইহার চারি হস্ত। দুইটি হস্ত ধ্যানমুদ্রাযুক্ত ও বক্ষোদেশের নিম্নভাগে সংন্যস্ত। তৃতীয় হস্তে অক্ষমালা ও চতুর্থ হস্তে পুঁথি। ইনি সম্ভবত মহামায়া অথবা ত্রিপুরভৈরবী।
দেবীর রুদ্রভাবদ্যোতক অনেক মূৰ্ত্তি পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে মহিষমর্দিনীই সমধিক প্রসিদ্ধ। বর্ত্তমানে শরৎকালে বাংলায় যে দুর্গার পূজা হয়, তাহা এই মহিষ মর্দিনীর মূৰ্ত্তি হইতেই উদ্ভূত। এই মূর্ত্তি কেবল ভারতের সৰ্ব্বত্র নহে, সুদূর যবদ্বীপেও সুপরিচিত ছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডী অধ্যায়ে এই দেবীর সবিশেষ বিবরণ আছে। অষ্ট অথবা দশভুজা সিংহবাহিনী দেবী সদ্য নিহত মহিষের দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত অসুরের সহিত যুদ্ধে নিরত, তাঁহার হস্তে ত্রিশূল, খেটক, শর, খড়গ, ধনু, পরশু, অঙ্কুশ, নাগপাশ প্রভৃতি আয়ুধ। দিনাজপুর জিলার পোর্শা গ্রামে নবদুর্গার মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যস্থলে একটি বড় এবং চতুস্পার্শ্বে ক্ষুদ্র আটটি মহিষ-মর্দিনীর মূৰ্ত্তি। বড় মূর্ত্তিটির অষ্টাদশ এবং ক্ষুদ্র মূর্ত্তিগুলির ষোড়শ ভুজ। ভবিষ্যৎ পুরাণে এই দেবীর বর্ণনা আছে। দিনাজপুরের বেত্রা গ্রামে ৩২টি হস্তবিশিষ্টা অসুরের সহিত যুদ্ধরতা একটি দেবীর মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। কোনো গ্রন্থেই ইহার বর্ণনা নাই এবং এরূপ অন্য কোনো মূৰ্ত্তিও এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। বাখরগঞ্জের অন্তর্গত শিকারপুর গ্রামে পূজিতা উগ্রতারা দেবীমূৰ্ত্তির চারি হস্তে খড়গ, তরবারি, নীলোৎপল ও নরমুণ্ড। শবের উপর দণ্ডায়মান দেবীমূর্ত্তির উপরিভাগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, কার্তিক ও গণেশের মূর্ত্তি উৎকীর্ণ।
বাংলায় পাশাপাশি উত্তীর্ণ সপ্তমাতৃকার মুক্তিযুক্ত প্রস্তরখণ্ড অনেক পাওয়া গিয়াছে। এই মাতৃকাগণ দেবগণের শক্তিরূপে কল্পিত। ইঁহাদের নাম ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী, বারাহী ও চামুণ্ডা। চামুণ্ডার পৃথক ও বিভিন্ন রূপের মূর্ত্তি অনেক পাওয়া যায়। ইহার কোনো কোনোটি ষড়ভুজা, নানা আয়ুধধারিণী ও নৃত্যপরায়ণা। বর্দ্ধমান জিলার অট্টহাস গ্রামে চামুণ্ডা দেবীর দম্ভরারূপের এক অদ্ভুত মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহার অতি ক্ষীণ শীর্ণ দেহ, গোলাকৃতি চক্ষু, বিকশিত দন্ত, পৈশাচিক হাস্য, কোটরগত জঠর ও ঊৰ্দ্ধজানু হইয়া বসিবার ভঙ্গী-সকলই একটা অদ্ভুত ভৌতিক রহস্যের দ্যোতক।
চামুণ্ডা ব্যতীত ব্রহ্মাণী, বারাহী ও ইন্দ্রাণী (চিত্র নং ২২ খ) এই তিন মাতৃকারও পৃথক মূৰ্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তবে তাহা সংখ্যায় অল্প।
প্রধান প্রধান ধর্ম্মমত ব্যতীত এদেশে অনেক লৌকিক ধৰ্ম্মানুষ্ঠান ও দেব দেবীর পূজা জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পরবর্ত্তীকালে এই সমুদয় দেব দেবী শিব অথবা বিষ্ণুর পরিবারভুক্ত বলিয়া গণ্য হইলেও আদিতে হঁহারা লৌকিক দেবতা মাত্র ছিলেন, এরূপ অনুমানই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এইরূপ যে সমুদয় দেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে মনসা, হারীতী, ষষ্ঠী, শীতলা প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। গঙ্গা ও যমুনার মূর্ত্তি সাধারণত মন্দিরের দরজার দুই পার্শ্বে খোদিত থাকে, কিন্তু তাঁহাদের পৃথক মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে (চিত্র নং ৯)।
বাংলা দেশে ও পূর্ব্ব ভারতের অন্যান্য প্রদেশে এক শ্রেণীর দেবীমূর্ত্তি বহুসংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। দেবী একটি শিশুপুত্র পার্শ্বে লইয়া শুইয়া আছেন এবং একটি কিঙ্করী তাঁহার পদসেবা করিতেছে। উৰ্দ্ধদেশে শিবলিঙ্গ এবং কার্তিক, গণেশ ও নবগ্রহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি। কেহ কেহ ইহাকে কৃষ্ণ-যশোদার মূর্ত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, শিশুটি সদ্যোজাত শিবের মূর্ত্তি।
.
৪. অন্যান্য পৌরাণিক দেবমূর্ত্তি
রাজসাহী জিলার অন্তর্গত কুমারপুর ও নিয়ামপুরে যে দুইটি সূৰ্য্যমূৰ্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাহা গুপ্তযুগে নির্ম্মিত বলিয়া অনুমিত হয়। এই প্রাচীন মূর্ত্তিতে সূর্যের দুই হস্ত সনাল পদ্ম, দুই পার্শ্বে অনুচর ও পাদপীঠে সপ্তাশ্ব উত্তীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। বগুড়া জিলার দেওড়া গ্রামে প্রাপ্ত রথারূঢ় সূৰ্য্যমূর্ত্তিতে সারথি অরুণের দুই পার্শ্বে দণ্ডী ও পিঙ্গল নামক দুই অনুচর ব্যতীত শরনিক্ষেপকারিণী ঊষা ও প্রত্যুষা নামে দুই দেবী আছেন। পরবর্ত্তীকালের সূৰ্য্যমূৰ্ত্তিতে সংজ্ঞা ও ছায়া নামে সূর্যের দুই রাণী ও মহাশ্বেতা নামে আর এক পার্শ্বচারিণীর মূর্ত্তি এবং মূল মূর্ত্তির বক্ষোদেশ উপবীত ও পদদ্বয়ে জুতা দেখা যায় (চিত্র নং ১৫-১৭)। সূৰ্য্যমূৰ্ত্তি সাধারণত দ্বিভুজ কিন্তু দিনাজপুরের অন্তর্গত মহেন্দ্র নামক স্থানে একটি ষড়ভুজ সূৰ্য্যমূৰ্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। দক্ষিণ ভারতের সূৰ্য্যমূর্ত্তির ন্যায় বাংলার কৃচিৎ দুই-একটি মূর্ত্তিতে জুতা দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজসাহী জিলার অন্তর্গত মান্দায় প্রাপ্ত একটি সূৰ্য্যমূর্ত্তির তিনটি মুখ ও দশটি বাহু। পার্শ্বের দুইটি মুখের ভাব অতিশয় উগ্র ও দশ বাহুতে শক্তি, খট্টাঙ্গ, ডমরু প্রভৃতি দেখিয়া অনুমিত হয় যে ইহা মার্তণ্ড-ভৈরবের মূর্ত্তি। কিন্তু শারদাতিলক তন্ত্র অনুসারে মার্তণ্ড-ভৈরবের চারিটি মুখ।
পুরাণ অনুসারে রেবন্ত সূর্যের পুত্র। রেবন্তের কয়েকটি মূৰ্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। দিনাজপুর জিলার ঘাটনগরে প্রাপ্ত মূর্ত্তিটি বুটজুতা-পরিহিত ও অশ্বারূঢ়; এক হস্তে কশা, অন্য হস্তে অশ্বের বলগা; একটি অনুচর দেবমূৰ্ত্তির মস্তকে ছত্র ধারণ করিয়া আছে; সম্মুখ হইতে একটি ও পশ্চাতে বৃক্ষের উপর হইতে আর একটি দস্যু রেবন্তকে আক্রমণ করিতে উদ্যত। ত্রিপুরা জিলায় বড়কামতা গ্রামে প্রাপ্ত ভগ্ন একটি মূর্ত্তিতে অশ্বারূঢ় রেবন্তের হস্তে একটি পাত্র এবং তাঁহার পশ্চাতে কুকুর, বাদক ও অনুচরের দল। সম্ভবত এটি মৃগয়াযাত্রার দৃশ্য। বৃহৎসংহিতা ও অন্যান্য গ্রন্থে রেবন্তের এইরূপ বর্ণনা আছে। ঘাটনগরের মূর্ত্তিটি মার্কণ্ডেয় পুরাণের বর্ণনার অনুরূপ।
নবগ্রহের সহিতও সূর্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। নবগ্রহের মূৰ্ত্তি সাধারণত একসঙ্গে পৃথক কোনো প্রস্তরখণ্ডে অথবা অন্য কোনো দেবমূর্ত্তির পারিপার্শ্বিকরূপে উত্তীর্ণ দেখা যায়। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত কাকলদীঘি গ্রামে নবগ্রহের একটি সুন্দর মূৰ্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। নয়টি গ্রহদেবতা তাঁহাদের বিশিষ্ট লাঞ্ছন হস্তে এক পংক্তিতে দাঁড়াইয়া আছেন এবং তাঁহাদের বাহনগুলি যথাক্রমে পাদপীঠের নিম্নভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে। অগ্রভাগে গণেশের একটি মূর্ত্তি আছে। এই প্রকার নবগ্রহমূর্ত্তির সাহায্যেই সম্ভবত স্বস্ত্যয়ন অথবা গ্রহযোগ সম্পন্ন হইত। নবগ্রহের পৃথক পৃথক মূৰ্ত্তি বড় একটা পাওয়া যায় না। তবে পাহাড়পুরের প্রধান মন্দিরের তলভাগে যে সমুদয় প্রস্তরফলক আছে, তাহাতে চন্দ্র ও বৃহস্পতির দুইটি মূৰ্ত্তি উত্তীর্ণ আছে।
ইন্দ্র, অগ্নি, যম, বরুণ, কুবের প্রভৃতি দিকপালের মূৰ্ত্তিও পাহাড়পুরে ও বাংলার অন্যান্য স্থানে পাওয়া গিয়াছে।
.
৫. জৈনমূৰ্ত্তি
সাধারণত বাংলায় যে সকল দেবমূৰ্ত্তি পাওয়া যায়, তাহা অষ্টম শতাব্দীর পরবর্ত্তী। সম্ভবত ঐ সময় হইতেই বাংলায় জৈনধর্ম্মের প্রভাব ও প্রতিপত্তি খুবই কমিয়া যায় এবং এই কারণেই জৈনমূৰ্ত্তি বাংলায় খুব কমই পাওয়া গিয়াছে।
দিনাজপুর জিলার অন্তর্গত সুরহর গ্রামে তীর্থঙ্কর ঋষভনাথের একটি অপূৰ্ব্ব মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মন্দিরাকারে গঠিত শিলাপটের ঠিক মধ্যস্থলে বদ্ধপদ্মাসনে জিন ঋষভনাথ উপবিষ্ট, এবং পাদপীঠের নিম্নে তাঁহার বিশেষ লাঞ্ছন বৃষমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির উর্ধ্বে তিন সারিতে ও দুই পার্শ্বে দুই শ্রেণীতে অনুরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরে উপবিষ্ট অবশিষ্ট তেইশজন তীর্থঙ্করের ক্ষুদ্র মূর্ত্তি। মূল মূর্ত্তির দুই ধারে চৌরী হস্তে দুইজন অনুচর ও মস্তকের দুই পার্শ্বে মাল্যহস্তে দুইজন গন্ধৰ্ব্ব। এই সুন্দর মূর্ত্তিটি সূক্ষ্ম শিল্পজ্ঞানের পরিচায়ক এবং সম্ভবত পালযুগের প্রথমভাগে নির্ম্মিত। মেদিনীপুর জিলার বরভূমে ঋষভনাথের আর একটি মূৰ্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে কেন্দ্রস্থলে মূল মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে চব্বিশজন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি; সকলেই কায়োৎসর্গ মুদ্রায় দণ্ডায়মান।
বাঁকুড়ার অন্তর্গত দেউলভিরে জিন পার্শ্বনাথের একটি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। জিন যোগাসনে বসিয়া আছেন এবং তাঁহার মস্তকের উপর একটি সর্প সাতটি ফণা বিস্তার করিয়া আছে। চব্বিশ পরগণার কাঁটাবেনিয়ায় কায়োৎসর্গ মুদ্রায় দণ্ডায়মান একটি পার্শ্বনাথের মূর্ত্তির দুই পার্শ্বে অবশিষ্ট তেইশজন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি উত্তীর্ণ হইয়াছে।
বর্দ্ধমান জিলার উজানী গ্রামে জিন শান্তিনাথের একটি দণ্ডায়মান মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। পাদপীঠে তাঁহার বিশেষ লাঞ্ছন মৃগ এবং পশ্চাতে নবগ্রহের মূর্ত্তি খোদিত।
.
৬. বুদ্ধমূর্ত্তি
বাংলা দেশে যে সমুদয় বুদ্ধমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, তাঁহার মধ্যে রাজশাহী জিলার অন্তর্গত বিহারৈল গ্রামে প্রাপ্ত একটি মূর্ত্তি সর্বপ্রাচীন। ইহা গুপ্তযুগে নির্ম্মিত সারনাথের বুদ্ধমূর্ত্তিগুলির অনুরূপ।
খুলনা জিলার অন্তর্গত শিববাটি গ্রামে শিবরূপে পূজিত একটি মূর্ত্তি (চিত্র নং ২৭ খ) পরবর্ত্তীকালের বুদ্ধমূর্ত্তির একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত। জটিল ও বিচিত্র কারুকার্যখচিত প্রস্তরখণ্ডের মধ্যস্থলে মন্দিরের মধ্যে বুদ্ধ ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট। বুদ্ধের জীবনের প্রধান প্রধান কতকগুলি ঘটনা–জন্ম, প্রথম উপদেশ, মহাপরিনির্বাণ, নালাগিরি-দমন, ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গ হইতে অবতরণ প্রভৃতি-মূল মূর্ত্তির প্রভাবলীতে খোদিত। এই ঘটনাগুলি পৃথকভাবেও খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়।
মহাযান ও বজ্রযান সম্প্রদায় যে পালযুগে এদেশে বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল, এই দুই মতের অনুযায়ী বহুসংখ্যক দেব-দেবীর মূর্ত্তিই তাঁহার সাক্ষ্য প্রদান করে। ইঁহাদের মধ্যে ধ্যানীবুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর (অথবা লোকেশ্বর) (চিত্র নং ২১ খ) ও মঞ্জুশ্রী নামক দুই বোধিসত্ত্ব, এবং তারা কয়েকটি প্রধান এবং জম্ভল, হেরুক ও হেবজ্র এই কয়টি অপ্রধান।
ধ্যানীবুদ্ধের মূৰ্ত্তি খুব বেশী পাওয়া যায় নাই। ঢাকা জিলার সুখবাসপুরে বজ্ৰসত্ত্বের একটি মূৰ্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। বীরাসনে উপবিষ্ট এই মূর্ত্তিটির দক্ষিণ হস্তে বজ্র এবং বাম হস্তে ঘণ্টা। পশ্চাদ্ভাগে উত্তীর্ণ লিপি হইতে অনুমিত হয় যে, মূর্ত্তিটি দশম শতাব্দীতে নির্ম্মিত।
অবলোকিতেশ্বরের বহুসংখ্যক এবং খসর্পণ, সুগতি-সন্দর্শন, ষড়ক্ষরী প্রভৃতি বহুশ্রেণীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ঢাকা জিলার মহাকালীতে একাদশ শতাব্দীতে নিৰ্মিত খসর্পণের একটি অতিশয় সুন্দর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়ছে। সপ্তরথ পাদপীঠের উপর সনাল-পদ্ম-হস্তে ললিতাসনে উপবিষ্ট অবলোকিতেশ্বর যেন পরমকরুণাভরে পৃথিবী অবলোকন করিতেছেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে তারা ও সুধনকুমার এবং বাম পার্শ্বে ভূকুটী ও হয়গ্রীব পৃথক পৃথক পদ্মের উপরে আসীন। ঊর্ধ্বে প্রভাবলীতে পাঁচটি মন্দিরাভ্যন্তরে পঞ্চতথাগতের ধ্যানমূৰ্ত্তি এবং নিম্নে পাদপীঠে সূচীমুখমূর্ত্তি এবং নানা রত্ন ও উপচার খোদিত। রাজসাহী চিত্রশালায় ষড়ভুজ লোকেশ্বরের যে মূৰ্ত্তি আছে তাহা সম্ভবত সুগতি-সন্দর্শন লোকেশ্বর। ইঁহার এক হস্তে বরদমুদ্রা এবং এবং অন্য পাঁচ হস্তে পুঁথি, পাশ, ত্রিদণ্ডী (অথবা ত্রিশূল), অক্ষমালা এবং কমণ্ডলু। মালদহ জিলায় বাণীপুরে প্রাপ্ত ষড়ক্ষরী লোকেশ্বরের মূর্ত্তি বজ্ৰপৰ্য্যঙ্ক আসনে উপবিষ্ট ও চতুর্ভুজ; দুই হস্ত অঞ্জলিবদ্ধ ও অপর দুই হস্তে অক্ষমালা ও পদ্ম। মূর্ত্তির মস্তকে বজ্রমুকুট এবং দুই পার্শ্বে মণিধর ও ষড়ক্ষরী মহাবিদ্যার ক্ষুদ্র মূর্ত্তি।
মহাস্থানের নিকটে বলাইধাপে একটি সুন্দর মঞ্জুশ্রীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটি অষ্টধাতুনির্ম্মিত কিন্তু স্বর্ণপটে আচ্ছাদিত, এবং ইহার মস্তকের জটামধ্যে ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্যের মূর্ত্তি। দ্বিভঙ্গ ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান মঞ্জুশ্রীর বাম হস্তে ব্যাখ্যান বা বিতর্ক-মুদ্রা-কারণ ইনি হিন্দু দেবতা ব্রহ্মার ন্যায় জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের আকর। পরিহিত ধুতি মেখলা দ্বারা আবদ্ধ এবং চাদরখানি উপবীতের ন্যায় বাম স্কন্ধের উপর দিয়ে দেহের ঊর্ধ্বভাগ বেষ্টন করিয়া আছে। ঢাকা জিলার জালকুণ্ডী গ্রামে মঞ্জুশ্রীর অরপচন রূপের একখানি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তরবারিধৃত দক্ষিণ হস্ত খানির অগ্রভাগ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; বাম হস্তে বুকের নিকট একখানা পুঁথি ধরিয়া আছেন। চারপাশে জালিনী, উপকেশিনী, সূৰ্য্যপ্রভা ও চন্দ্রপ্রভা নামে তাঁহার চারিটি ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি এবং প্রভাবলীর উপরিভাগে বৈরোচন, অক্ষোভ্য, অমিতাভ ও রত্নসম্ভব এই চারিটি ধ্যানীবুদ্ধের মূর্ত্তি।
বৌদ্ধ দেবতা জম্ভল পৌরাণিক দেবতা কুবেরের ন্যায় যক্ষগণের অধিপতি ও ধনসম্পদের অধিষ্ঠাত্ দেবতা। বাংলায় বহু জলমূৰ্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। স্থূলোদর এই মূৰ্ত্তির দক্ষিণ হস্তে অক্ষমা; বাম হস্তে একটি নকুলের গলা টিপিয়া ইহার মুখ হইতে ধন-রত্ন বাহির করিতেছেন। মূর্ত্তির নিম্নে একটি ধনপূর্ণ ঘট উপুড় হইয়া আছে।
হেরুকের মূৰ্ত্তি খুব কমই পাওয়া যায়। ত্রিপুরা জিলার শুভপুর গ্রামে হেরুকের একটি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। নৃত্যপরায়ণ, দংষ্ট্ৰাকরালবদন এই মূর্ত্তির বাম হস্তে কপাল ও দক্ষিণ হস্তে বজ্ৰ; মস্তকে ধ্যানীবুদ্ধ অক্ষোভ্যের মূর্ত্তি, গলদেশে নরমুণ্ডমালা এবং বাম স্কন্ধে খট্বাঙ্গ।
হেবজ্রের একটি মূর্ত্তি মুর্শিদাবাদে পাওয়া গিয়াছে। শক্তির সহিত নিবিড় আলিঙ্গনাবদ্ধ দণ্ডায়মান মূর্ত্তির আট মস্তক ও ষোলো হাত; প্রতি হাতে একটি নরকপাল ও পদতলে কতকগুলি নর-শব।
মহাযান ও বজ্রযানে উপাস্যা দেবীর সংখ্যা অনেক। তন্মধ্যে প্রজ্ঞাপারমিতা, মারীচী, পর্ণশবরী, চুণ্ডা ও হারীতী এবং বিভিন্ন ধ্যানীবুদ্ধ হইতে প্রসূত বিভিন্ন তারা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রজ্ঞাপারমিতা দিব্যজ্ঞানের প্রতীক। তাঁহার মূর্ত্তি কমই পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু অনেক প্রজ্ঞাপারমিতা-পুঁথির আচ্ছাদনের উপর তাঁহার ছবি উজ্জ্বল ও নানা রঙ্গে চিত্রিত আছে। পদ্মাসনে আসীনা দেবীর মুখমণ্ডলে জ্ঞানের দীপ্তি, এবং বক্ষোদেশ-সন্নদ্ধ এক হস্তে ব্যাখ্যান-মুদ্রা, অপর হস্তে জ্ঞানমুদ্রা ও প্রজ্ঞাপারমিতা-পুঁথি দেখিতে পাওয়া যায়।
মারীচীর তিন মুখ (একটি শূকরীর মুখ); আট হাতে বজ্র, অঙ্কুশ, শর, অশোকপত্র, সূচী, ধনু, পাশ ও তর্জনীমুদ্রা; মস্তকে ধ্যানীবুদ্ধ বিরোচনের মূর্ত্তি। সূৰ্য্যের ন্যায় তিনি প্রত্যূষের দেবী। সারথি রাহুচালিত সপ্তশূকরবাহিত রথে প্রত্যালীঢ় ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান মারীচী মূর্ত্তিই সাধারণত এদেশে পাওয়া যায়।
রাজসাহী যাদুঘরে অষ্টাদশভুজা একটি চুণ্ডা মূর্ত্তি আছে। বিক্রমপুরের পর্ণশবরীর দুইটি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহার তিনটি মাথা ও ছয়খানি হাত; হাতে বজ্র, পরশু, শর, ধনু, পর্ণপিচ্ছিক প্রভৃতি। কয়েকটি বৃক্ষপত্র ব্যতীত অন্য কোনো পরিধান নাই। সম্ভবত পার্ব্বত্য শবরজাতির উপাস্যা দেবী বৌদ্ধ দেবীতে পরিণত হইয়াছেন।
অমোঘসিদ্ধি, রত্নসম্ভব এবং অমিতাভ এই তিন ধ্যানীবুদ্ধ হইতে প্রসূত তারা যথাক্রমে শ্যামতারা, বজ্রতারা ও ভূকুটীতারা নামে পরিচিত। শ্যামতারার মূৰ্ত্তি খুব বেশী পাওয়া যায়। তাঁহার হাতে একটি নীলপদ্ম এবং পার্শ্বে অশোককান্তা ও একজটার মূর্ত্তি। ফরিদপুর জিলায় মাজবাড়ী গ্রামে অষ্টধাতুনির্ম্মিত একটি বজ্রতারার মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহা একটি পদ্মের আকার। পদ্মের কেন্দ্রস্থলে দেবীমূৰ্ত্তি এবং আটটি দলের মধ্যে তাঁহার আটটি অনুচরীর মূর্ত্তি। এই আটটি দল ইচ্ছা করিলে বন্ধ করিয়া রাখা যায়-তখন বাহির হইতে ইহা কেবলমাত্র একটি অষ্টদল পদ্ম বলিয়া মনে হয়। ঢাকা জিলার অন্তর্গত ভবানীপুর গ্রামে বীরাসনে উপবিষ্টা একটি দেবীমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহার তিন মাথা ও আট হাত। মূর্ত্তির মস্তকে অমিতাভ ও পাদপীঠে গণেশের মূৰ্ত্তি। কেহ কেহ মনে করেন যে, ইহা ভূকুটীতারার মূর্ত্তি।
এতদ্ভিন্ন আরও অনেক বৌদ্ধ দেবী বা শক্তিমূৰ্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। অষ্টভুজা একটি সুন্দর দেবীমূৰ্ত্তি কেহ কেহ সিতাপত্রা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আর একটি দেবীমূৰ্ত্তি মহাপ্রতিসরা (চিত্র নং ২১ গ) বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। কিন্তু প্রাচীন সাধনমালায় এই সমুদয় দেবীর যে বর্ণনা আছে, তাঁহার সহিত এই দুই মূর্ত্তির সামঞ্জস্য নাই।
১৮. সমাজের কথা
অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ – সমাজের কথা
জাতিভেদ
যে যুগে মনুস্মৃতি, মহাভারত প্রভৃতি রচিত হয়, সেই যুগেই যে আৰ্য্য ধর্ম্ম ও সামাজিক রীতিনীতি প্রভৃতি বাংলা দেশে প্রভাব বিস্তার করে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বেকার বাঙ্গালীর ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই অল্প। সামান্য যাহা কিছু জানা গিয়াছে, তাহাও সংক্ষেপে পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।
জাতিভেদ আৰ্যসমাজের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর্য্যগণ এদেশে বসবাস করিবার ফলে বাংলায়ও ইহার প্রবর্ত্তন হয়। ইহার ফলে বঙ্গ, সুহ্ম, শবর, পুলিন্দ, কিরাত, পুণ্ড প্রভৃতি বাংলার আদিম অধিবাসীগণ প্রাচীন গ্রন্থে ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য হয়। অল্পসংখ্যক বাঙ্গালী যে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইত ইহা খুবই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়, কিন্তু কোনো প্রাচীন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে দীর্ঘতমা ঋষির যে কাহিনী উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে, আৰ্য ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গালী কন্যা বিবাহ করিতেন। এইরূপ বিবাহের ফলেই আৰ্যপ্রভাব এদেশে পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল।
যে সমুদয় বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় হইয়াছিল, তাহারা সম্ভবত সংখ্যায় খুব বেশী ছিল না। বাংলার আদিম অধিবাসীদের অধিকাংশই শূদ্রজাতিভুক্ত হইয়াছিল। মনুসংহিতাতে উক্ত হইয়াছে যে পুণ্ড্রক এবং কিরাত এই দুই ক্ষত্রিয় জাতি ব্রাহ্মণের সহিত সংস্রব না থাকায় ও শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকৰ্ম্মাদির অনুষ্ঠান না করায় শূদ্রত্ব লাভ করিয়াছে। কৈবর্ত্তজাতি মনুসংহিতায় সংকর জাতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু বিষ্ণুপুরাণে অব্ৰহ্মণ্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সম্ভবত এইরূপে আরও অনেকের জাতি-বিপর্যয় ঘটিয়াছে। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে বাংলা দেশের জাতি বিভাগ বহু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।
খৃষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে যে এদেশে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহার পরবর্ত্তী সকল যুগেই যে এদেশে বহু ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার বহুবিধ প্রমাণ আছে। বাংলার বহু রাজবংশ-পাল, সেন, বৰ্ম প্রভৃতি তাঁহাদের লিপিতে ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এদেশে এরূপ একটি মত প্রচলিত আছে যে, বাংলায় কলিকালে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ছিল না, কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এই দুই বর্ণ ছিল। ইহার কোনো ভিত্তি নাই। প্রাচীনকালে বাংলায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণই ছিল এবং হিন্দু যুগের শেষভাগে বাংলায় রচিত প্রামাণিক শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদিতে চারি বর্ণেরই উল্লেখ এবং তাহাদের বৃত্তি প্রভৃতি নির্দিষ্ট আছে।
কিন্তু আৰ্যসমাজ আদিতে চারি বর্ণে বিভক্ত হইলেও ক্রমে বহুসংখ্যক বিভিন্ন জাতির সৃষ্টি হয়। যে সময় বাংলায় আৰ্যপ্রভাব বিস্তৃত হয়, সে সময় আৰ্যসমাজে এরূপ বহু জাতির উদ্ভব হইয়াছে। মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, বিভিন্ন বর্ণের পুরুষ ও স্ত্রীর সন্তান হইতেই এই সমুদয় মিশ্রবর্ণের সৃষ্টি হইয়াছে এবং কোন কোন বর্ণ অথবা জাতির মিশ্রণের ফলে কোন কোন মিশ্রবর্ণের সৃষ্টি হইল, তাঁহার সুদীর্ঘ তালিকা আছে। এই তালিকাগুলির মধ্যে অনেক বৈষম্য দেখা যায়। তাঁহার কারণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মিশ্রবর্ণের উদ্ভব হইয়াছিল। প্রতি ধৰ্ম্মশাস্ত্রে সাধারণত তৎকালে স্থানীয় সমাজে প্রচলিত মিশ্রবর্ণেরই উল্লেখ আছে, সুতরাং স্থান ও কাল অনুসারে এই মিশ্রবর্ণের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম্মশাস্ত্রে মিশ্রবর্ণেরই উৎপত্তির যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা যে অধিকাংশস্থলেই কাল্পনিক, সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু একথাও অস্বীকার করা কঠিন যে, এইরূপ ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়াই প্রধানত সমাজে এই সমুদয় মিশ্রবর্ণের উচ্চ-নীচ ভেদ নির্দিষ্ট হইয়াছে। বাংলা দেশের সমাজে যখন এই জাতিভেদ প্রথা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন ভারতের সর্বত্রই আৰ্যসমাজে আদিম চতুৰ্ব্বর্ণের পরিবর্তে এইরূপ মিশ্র জাতিই সমাজের প্রধান অঙ্গে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালী সমাজের প্রকৃত পরিচয় জানিতে হইলে, বাংলার এই মিশ্র জাতি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করার প্রয়োজন।
হিন্দু যুগে বাংলা দেশে রচিত কোনো শাস্ত্রগ্রন্থে মিশ্র জাতির তালিকা থাকিলে, বাংলার জাতিভেদ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ সম্ভবপর হইত, কিন্তু এরূপ কোনো গ্রন্থের অস্তিত্ব এখন পর্য্যন্ত সঠিকভাবে জানা যায় নাই। তবে বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ এই দুইখানি গ্রন্থ, হিন্দু যুগের না হইলেও, ইহার অবসানের অব্যবহিত পরেই রচিত, এবং ইহাতে মিশ্র জাতির যে বর্ণনা আছে, তাহা বাংলা দেশ সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য, এরূপ অনুমান করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। সুতরাং এই দুইখানি গ্রন্থের সাহায্যে বাংলা সমাজের জাতিভেদ-প্রথা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে, হিন্দু যুগের অবসানকালে ইহা কিরূপ ছিল, তাঁহার সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা করা যাইবে।
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দী বা তাঁহার অব্যবহিত পরে রচিত হইয়াছিল। ইহাতে ব্রাহ্মণের মাছ-মাংস খাওয়ার বিধি আছে এবং ব্রাহ্মণের সমুদয় লোককে ৩৬টি শূদ্র জাতিতে বিভক্ত করা হইয়াছে। এই দুইটিই বাংলা দেশের সমাজের বৈশিষ্ট্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কারণ আৰ্য্যাবর্তের অন্যত্র ব্রাহ্মণেরা নিরামিষাশী, এবং বাংলায় চলিত কথায় এখনো ছত্রিশ জাতির উল্লেখ আছে। এই গ্রন্থে পদ্মা ও বাংলার যমুনা নদীর উল্লেখও বাংলার সহিত ইহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সূচিত করে। তবে ব্রাহ্মণ ভিন্ন সকলেই যে শূদ্র-জাতীয়, ইহা সম্ভবত হিন্দু যুগের সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে; ইহার পরবর্ত্তী যুগের অর্থাৎ উক্ত গ্রন্থরচনাকালের ধারণা।
বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে রাজা বেন বর্ণাশ্রম ধৰ্ম্ম নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বলপূর্ব্বক বিভিন্ন বর্ণের নরনারীর সংযোগ সাধন করেন এবং ইহার ফলে বিভিন্ন মিশ্রবর্ণের উৎপত্তি হয়। এই মিশ্রবর্ণগুলি সবই শূদ্র-জাতীয় এবং উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন সংকর শ্রেণীতে বিভক্ত।
করণ, অন্বষ্ঠ, উগ্র, মাগধ, তন্ত্রবায়, গান্ধিকবণিক, নাপিত, গোপ (লেখক), কৰ্ম্মকার, তৌলিক (সুপারি-ব্যবসায়ী), কুম্ভকার, কুংসকার, শংখিক, দাস (কৃষিজীবী), বারজীবী, মোক, মালাকার, সূত, রাজপুত ও তামুলী এই কুড়িটি উত্তম সংকর।
তক্ষণ, রজক, স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক, আভীর তৈলকারক, ধীবর, শৌপ্তিক, নট, শাবাক, শেখর, জালিক-এই বারোটি মধ্যম সংকর। মলেগ্রহি, কুড়ব, চাণ্ডাল, বরুড়, তক্ষ, চর্মকার, ঘউজীবী, দোলাবাহী ও মল্ল এই নয়টি অধম সংকর, ইহারা অন্ত্যজ ও বর্ণাশ্রম-বহিষ্কৃত অর্থাৎ বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত নহে।
গ্রন্থে ৩৬টি জাতির উল্লেখ আছে-কিন্তু এই তালিকায় আছে ৪১টি; সুতরাং ৫টি পরবর্ত্তীকালে যোজিত হইয়াছে। যাহাদের পিতা-মাতা উভয়ই চতুৰ্বর্ণভুক্ত, তাহারা উত্তম সংকর; যাহাদের মাতা চতুৰ্ব্বর্ণভুক্ত কিন্তু পিতা উত্তম সংকর, তাহারা মধ্যম সংকর; এবং যাহাদের পিতা-মাতা উভয়ই সংকর, তাহারা অধম সংকর; এই সাধারণ বিধি অনুসারের উপরোক্ত তিনটি শ্রেণীবিভাগ পরিকল্পিত হইয়াছে। প্রত্যেক বর্ণেরই পৃথক বৃত্তি নির্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণেরা কেবলমাত্র উত্তম সংকর শ্রেণীভুক্ত বর্ণের পৌরোহিত্য করিবেন। অন্য দুই শ্রেণীর পুরোহিতেরা পতিত ব্রাহ্মণ বলিয়া গণিত এবং যজমানের বর্ণ প্রাপ্ত হইবেন। এতদ্ব্যতীত দেবল ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। গরুড় কর্ত্তৃক শকদ্বীপ হইতে আনীত বলিয়া ইহারা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হইতেন। দেবল পিতা ও বৈশ্য মাতার গর্ভজাত সন্তান গণক অথবা গ্রহবিপ্র। উপসংহারে উক্ত হইয়াছে যে বেনের দেহ হইতে ম্লেচ্ছ নামে এক পুত্র জন্মে এবং তাঁহার সন্তানগণ পুলিন্দ, পুস, খস, যবন, সুহ্ম, কম্বোজ, শবর, খর ইত্যাদি নামে খ্যাত হয়।
উল্লিখিত উত্তম ও মধ্যম সংকরভুক্ত বর্ণের অধিকাংশই এখনো বাংলায় সুপরিচিত জাতি। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ অনুসারে করণ ও অনুষ্ঠ সংকর বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অনুষ্ঠগণ চিকিৎসা ব্যবসায় করিত বলিয়া বৈদ্য নামেও অভিহিত হইয়াছে। করণেরা লিপিকর ও রাজকার্যে অভিজ্ঞ এবং সৎশূদ্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। এই করণই পরে বাংলায় কায়স্থ জাতিতে পরিণত হইয়াছে। এখনো বাংলা দেশে ব্রাহ্মণের পরেই বৈদ্য ও কায়স্থ উচ্চ জাতি বলিয়া পরিগণিত হয়। শঙ্কার, দাস (কৃষিজীবী), তন্তুবায়, মোদক, কর্ম্মকার ও সুবর্ণবণিক জাতি বাংলায় সুপরিচিত, কিন্তু বাংলার বাহিরে বড় একটা দেখা যায় না। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ যে প্রাচীন বাংলার সমাজ অবলম্বনে লিখিত এই সমুদয় কারণেও তাহা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে মিশ্রবর্ণের যে তালিকা আছে তাঁহার সহিত বৃহদ্ধৰ্ম্মোক্ত তালিকার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। তবে কিছু কিছু প্রভেদও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে প্রথমে গোপ, নাপিত, ভিলু, মোদক, কুবর, তামুলি, স্বর্ণকার ও বণিক ইত্যাদি সৎশূদ্র বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, এবং ইহার পরই করণ ও অমৃষ্ঠের কথা আছে। তৎপর বিশ্বকর্মার ঔরসে শূদ্রা-গর্ভজাত নয়টি শিল্পকার জাতির উল্লেখ আছে। ইহাদের মধ্যে মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্কার, কুবিন্দক (তন্তুবায়), কুম্ভকার ও কংসকার এই ছয়টি উত্তম শিল্পী জাতি। কিন্তু স্বর্ণ চুরির জন্য স্বর্ণকার ও কর্তব্য অবহেলার জন্য সূত্রধর ও চিত্রকর এই তিনটি শিল্পী জাতি ব্রহ্মশাপে পতিত। স্বর্ণকারের সংসর্গহেতু এবং স্বর্ণ চুরির জন্য এক শ্রেণীর বণিকও (সম্ভবত সুবর্ণবণিক) ব্রহ্মশাপে পতিত। ইহার পর পতিত সংকর জাতির এক সুদীর্ঘ তালিকার মধ্যে অট্টালিকাকার, কোটক, তীবর, তৈলকার, লেট, মল্ল, চর্মকার, শুণ্ডী, পৌণ্ড্রক, মাংসচ্ছেদ, রাজপুত্র, কৈবত্ত (কলিযুগে ধীবর), রজক, কৌয়ালী, গঙ্গাপুত্র, যুঙ্গী প্রভৃতির নাম আছে। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণোক্ত অধিকাংশ উত্তম ও মধ্যম সংকর জাতিই ব্রহ্মবৈবর্তে সৎশূদ্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। বৃহদ্ধৰ্ম্মের ন্যায় ইহাতেও নানাবিধ ম্লেচ্ছজাতির কথা আছে। ইহারা বলবান, দুরন্ত, অবিদ্ধকৰ্ণ, কুর, নির্ভয়, রণদুর্জয়, দুর্ধর্ষ, ধৰ্ম্মবর্জিত ও শৌচাচার-বিহীন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ব্যাধ, ভড়, কোল, কোঞ্চ, হচ্ছি, ডোম, জোলা, বাগতাত (বাগাদি?), ব্যালগ্রাহী (বেদে?) এবং চাণ্ডাল প্রভৃতি যে সমুদয় নীচ জাতির উল্লেখ আছে তাঁহার প্রায় সমস্তই এখনো বাংলা দেশে বর্ত্তমান। উপসংহার ব্রহ্মবৈবর্তে বৈদ্য জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এক বিস্তৃত আখ্যান এবং গণক ও অগ্রদানী ব্রাহ্মণের পাণ্ডিত্যের কারণ উল্লিখিত হইয়াছে।
বল্লালচরিতে যে সমুদয় আখ্যান উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতে মনে হয় যে রাজা মনে করিলে কোনো জাতিকে উন্নত অথবা অবনত করিতে পারিতেন। কিন্তু পালরাজগণের লিপিতে তাঁহাদের বর্ণাশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালনের উল্লেখ হইতে প্রমাণিত হয় যে সাধারণত রাজগণ সমাজের বিধান সযত্নে রক্ষা করিয়া চলিতেন; বিশেষত রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে কোনোরূপ গুরুতর পরিবর্ত্তন সহজসাধ্য ছিল না। অবশ্য কালক্রমে এরূপ পরিবর্ত্তন নিশ্চয়ই অল্পবিস্তর হইয়াছে। কিন্তু বৃহদ্ধর্ম্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে সামাজিক জাতিভেদের যে চিত্র পাওয়া যায় তাঁহার সহিত বর্ত্তমানকালের প্রভেদ এতই কম যে, হিন্দু যুগের অবসানে বাঙ্গালী সমাজের এই সমুদয় বিভিন্ন জাতি-অন্তত ইহার অধিকাংশই-যে বর্ত্তমান ছিল এবং তাহাদের শ্রেণীবিভাগ যে মোটামুটি একই প্রকারের ছিল তাহা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে।
প্রাচীন শাস্ত্রমতে সমাজের প্রত্যেক জাতিরই নির্দিষ্ট বৃত্তি ছিল। কিন্তু ইহা যে খুব কঠোরভাবে অনুসরণ করা হইত না তাঁহার বহু প্রমাণ আছে। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন-ইহাই ছিল ব্রাহ্মণের নির্দিষ্ট কৰ্ম্ম। কিন্তু সমসাময়িক লিপি হইতে জানা যায় যে, ব্রাহ্মণেরা রাজ্যশাসন ও যুদ্ধ বিভাগে কাৰ্য্য করিতেন। এইরূপ আমরা দেখিতে পাই যে কৈবর্ত্ত উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন, করণ যুদ্ধ ও চিকিৎসা করিতেন, বৈদ্য মন্ত্রীর কাজ করিতেন এবং দাসজাতীয় ব্যক্তি রাজকর্ম্মচারী ও সভাকবি ছিলেন।
বিভিন্ন জাতির মধ্যে অনুগ্রহণ ও বৈবাহিক সম্বন্ধ বিষয়ে উনবিংশ শতাব্দীর ন্যায় কঠোরতা প্রাচীন হিন্দু যুগে ছিল না। একজাতির মধ্যেই সাধারণত বিবাহাদি হইত, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর বর ও নিম্নশ্রেণীর কন্যার বিবাহ শাস্ত্রে অনুমোদিত ছিল এবং কখনো কখনো সমাজে অনুষ্ঠিত হইত। শিলালিপিতে স্পষ্ট প্রমাণ আছে যে ব্রাহ্মণ শূদ্রকন্যা বিবাহ করিতেন, এবং তাঁহাদের সন্তান সমাজে ও রাজদরবারে বেশ সম্মান লাভ করিতেন। সামন্তরাজ লোকনাথ ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু তাঁহার মাতামহ ছিলেন পারশব অর্থাৎ ব্রাহ্মণ পিতা ও শূদ্রা মাতার সন্তান। কিন্তু পারশব হইলেও তিনি সেনাপতির পদ অলঙ্কৃত করিতেন। হিন্দু যুগের শেষ পর্য্যন্ত যে এইরূপ বিবাহ প্রচলিত ছিল ভট্টভবদেব ও জীমূতবাহনের গ্রন্থ হইতে তাহা বেশ বোঝা যায়। তবে দ্বিজাতির শূদ্রকন্যা বিবাহ যে ক্রমশ নিন্দনীয় হইয়া উঠিয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।
বিভিন্ন জাতির মধ্যে পান ও ভোজন সম্বন্ধে নিষেধের কঠোরতাও এইরূপ আস্তে আস্তে গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন স্মৃতি অনুসারে সাধারণত কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের অন্ন ও জল গ্রহণ করিতেন না, এবং এই বিধিও খুব কঠোরভাবে প্রতিপালিত হইত না। এ সম্বন্ধে হিন্দু যুগের অবসানকালে বাংলা সমাজের কিরূপ বিধি প্রচলিত ছিল ভবদেবভট্ট প্রণীত ‘প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ’ গ্রন্থে তাঁহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।
ভবদেব বিধান করিয়াছেন যে চাণ্ডালস্পৃষ্ট ও চাণ্ডালদি অন্ত্যজ জাতির পাত্রে রক্ষিত জল পান করিলে ব্রাহ্মণাদি চতুৰ্ব্বণের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। শূদ্রের জল পান করিলে ব্রাহ্মণের সামান্য প্রায়শ্চিত্ত করিলে শুদ্ধি হইত। ব্রাহ্মণেতর জাতির পক্ষে এরূপ কোনো নিষেধ দেখা যায় না।
অন্ন বিষয়েও কেবল চাণ্ডালস্পৃষ্ট এবং চাণ্ডাল, অন্ত্যজ ও নটনৰ্তকাদি কতকগুলি জাতির পক্ অন্ন বিষয়ে নিষেধের ব্যবস্থা আছে। আপস্তম্বের একটি শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করিলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ভবদেব এই শ্লোকের উল্লেখ করিয়া নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য করিয়াছেন : ব্রাহ্মণ বৈশ্যান্ন গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্তের মাত্রা চতুর্থাংশ কম এবং ক্ষত্রিয়ান্ন গ্রহণ করিলে অর্ধেক; ক্ষত্রিয় শূদ্ৰান্ন ভোজন করিলে প্রায়শ্চিত্তের মাত্রা চতুর্থাংশ কম ও বৈশ্যান্ন গ্রহণ করিলে অর্ধেক; এবং বৈশ্য শূদ্ৰান্ন গ্রহণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত অর্ধেক–এইরূপ বুঝিতে হইবে। ভবদেব যে মূল শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহাতে কিন্তু এরূপ কোনো কথা নাই, এবং এই উক্তির সমর্থক অন্য কোনো শাস্ত্রবাক্য থাকিলে ভবদেব নিশ্চয়ই তাঁহার উল্লেখ করিতেন। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে শূদ্র ও অন্ত Uজ ব্যতীত অন্য জাতির অনুগ্রহণ করা পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের পক্ষেও নিষিদ্ধ ছিল না; ক্রমে হিন্দু যুগের অবসানকালে এই প্রথা ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিতেছিল। ভবদেব-শূদ্রের কন্দুপক্ক, তৈল-পক্ক, পায়েস, দধি প্রভৃতি ভোজ্য গ্রহণীয়-হারীতের এই উক্তি এবং আপস্তম্বের একটি বচন সমর্থন করিয়াছেন-তাহাতে বলা হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ যদি আপকালে শূদ্রের অন্ন ভোজন করেন তাহা হইলে মনস্তাপ দ্বারাই শুদ্ধ হন। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী স্মাৰ্ত্ত ভবদেবভট্টের এই সমুদয় উক্তি হইতে অনুমিত হয় যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে পান-ভোজন সম্বন্ধে নিষেধ তখনো পরবর্ত্তীকালের ন্যায় কঠোর রূপ ধারণ করে নাই এবং চাণ্ডালান্ন গ্রহণ করিলেও ব্রাহ্মণের জাতিপাত হইত না-প্রায়শ্চিত্ত করিলেই শুদ্ধি হইত।
.
২. ব্রাহ্মণ
হিন্দু যুগে বাংলায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির সম্বন্ধে বিস্তৃত কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রাচীনকাল হইতেই যে এদেশে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গুপ্তযুগে বাংলার সর্বত্র ব্রাহ্মণের বসবাসের কথা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। তাম্রশাসন ও শিলালিপি হইতে দেখা যায় যে, পরবর্ত্তীকালে বিদেশ হইতে আগত বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ এদেশে স্থায়ীভাবে বাস করিয়াছেন, আবার এদেশ হইতেও বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ অন্য দেশে গিয়াছেন। কালক্রমে বাংলার ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক, শাসদ্বীপী প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছিলেন। রাজা অথবা ধনীলোক ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি, কখনো বা সমস্ত গ্রাম, দান করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতেন। এই সমুদয় গ্রামের নাম হইতে ব্রাহ্মণদের গাঁঞীর সৃষ্টি হয় এবং ইহা তাঁহাদের নামের শেষে উপাধিস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। এইরূপে বন্দ্যঘটী, মুখটী, গাঙ্গুলী প্রভৃতি গ্রামের নাম ও গাঁঞী হইতে বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি সুপরিচিত উপাধির সৃষ্টি হইয়াছে। পুতিতুণ্ড, পিপলাই, ভট্টশালী, কুশারী, মাসচটক, বটব্যাল, ঘোষাল, মৈত্র, লাহিড়ী প্রভৃতি উপাধিও এইরূপে উদ্ভূত হইয়াছে। হিন্দু যুগের অবসানের পূর্ব্বেই যে বাংলায় ব্রাহ্মণদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ এবং গাঁঞীপ্রথা প্রচলিত ছিল তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু বাংলার কুলজী গ্রন্থে ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে বিস্তৃত বিবরণ আছে তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।
রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে কুলজীর উক্তি সংক্ষিপ্ত এই :
“গৌড়ের রাজা আদিশূর বৈদিক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবার জন্য কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, কারণ বাংলার ব্রাহ্মণেরা বেদে অনভিজ্ঞ ছিলেন। এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ স্ত্রীপুত্রাদিসহ বাংলা দেশে বসবাস করেন এবং আদিশূর তাঁহাদের বাসের জন্য পাঁচখানি গ্রাম দান করেন। কালক্রমে এই পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তানগণমধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইল এবং তাঁহার ফলে কতক রাঢ়দেশে ও কতক বরেন্দ্রভূমে বাস করিতে লাগিলেন। পরে মহারাজা বল্লালসেনের রাজ্যকালে বাসস্থানের নাম অনুসারের তাঁহারা রাঢ়ী এবং বারেন্দ্র নামে দুইটি নির্দিষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত হইলেন। কালক্রমে তাঁহাদের বংশধরেরা সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইল। আদিশূরের পৌত্র ক্ষিতিশূরের সময় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মোট সংখ্যা হয় ঊনষাট। ক্ষিতিশূর তাঁহাদের বাসের জন্য উনষাটুখানি গ্রাম দান করেন। এই সমুদয় গ্রামের নাম হইতেই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের গাঁঞীর উৎপত্তি হইয়াছে। রাজা ক্ষিতিশূরের পুত্র ধরাশূর এই সমুদয় ব্রাহ্মণদিগকে মুখ্য কুলীন, গৌণ কুলীন এবং শ্রোত্রীয় এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ মহারাজা বল্লালসেনের সময়ে কুলীন, শ্রোত্রীয় ও কাপ এই তিন ভাগে বিভক্ত হন। তাঁহাদের গাঁঞীর সংখ্যা একশত”।
উপরে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল তাঁহার প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে বিভিন্ন কুলজী গ্রন্থের মধ্যে গুরুতর প্রভেদ বর্ত্তমান। মহারাজা আদিশূরের বংশ ও তারিখ, পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম ও আনয়নের কারণ, বঙ্গদেশে তাঁহাদের প্রতিষ্ঠা, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণীর উৎপত্তির কারণ, গাঁঞীর নাম ও সংখ্যা, কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তনের কারণ ও বিবর্ত্তনের ইতিহাস প্রভৃতি প্রত্যেক বিষয়েই পরস্পরবিরোধী বহু উক্তি বিভিন্ন কুলগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমুদয় কুলগ্রন্থের কোনোখানিই খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দের পূর্ব্বে রচিত নহে। সুতরাং এই সমুদয় গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের ইতিহাস রচনা করা কোনোমতেই সমীচীন নহে। কুলজীর মতে আদিশূর কর্ত্তৃক পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়নের পূৰ্ব্বে বাংলায় মাত্র সাতশত ঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহাদের বংশধরেরা সপ্তশতী নামে খ্যাত ছিলেন এবং ব্রাহ্মণসমাজে বিশেষ হীন বলিয়া বিবেচিত হইতেন। কালক্রমে সাতশতী ব্রাহ্মণ বাংলাদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং পরবর্ত্তীকালে আগত বৈদিক প্রভৃতি কয়েকটি বিশিষ্ট শ্রেণীর অতি অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণ ব্যতীত বাংলা দেশের প্রায় সকল ব্রাহ্মণই কান্যকুব্জ হইতে আগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তান। এই উক্তি বা প্রচলিত মত বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন বা ততোধিক ব্রাহ্মণ এদেশে আসিয়াছিলেন ইহা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। কারণ তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে মধ্যদেশ হইতে আগত বহু ব্রাহ্মণ এদেশে ও ভারতের অন্যত্র স্থায়ীভাবে বসবাস করিয়াছেন। ইঁহারা বাংলা দেশের ব্রাহ্মণদের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন, এবং বাসস্থানের নাম অনুসারে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র প্রভৃতি বিভিন্ন ব্রাহ্মণ শ্রেণীর উদ্ভব হইয়াছে, ইহাই সঙ্গত ও স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত বলিয়া মনে হয়। কৌলীন্য মৰ্য্যাদার উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কুলগ্রন্থের বর্ণনাও অধিকাংশই কাল্পনিক ও অতিরঞ্জিত।
বাংলার বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সংখ্যায় অল্প হইলেও বিশেষ সম্মানভাজন। ইঁহারা দাক্ষিণাত্য ও পাশ্চাত্য এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের ন্যায় ইহাদের কোনো গাঁঞী বা কৌলীন্যপ্রথা নাই।
দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণের মতে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা উৎকল, দ্রাবিড় প্রভৃতি দেশ হইতে আসিয়া বাংলায় বসবাস করেন। ইঁহারা বলেন যে আর্য্যাবর্তে মুসলমানদিগের রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইলে সেখানে বেদাদি শাস্ত্রচর্চ্চার ক্রমশ হ্রাস হইল। কিন্তু দ্রাবিড়াদি দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বেদের বিলক্ষণ চর্চ্চা থাকায় বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ তাহাদিগকে সাদরে স্বদেশে বাস করাইলেন।
পাশ্চাত্য বৈদিকগণের কুলগ্রন্থে তাঁহাদের যে বিবরণ পাওয়া যায় তাহা সংক্ষিপ্ত এই :
“গৌড়দেশের রাজা শ্যামলবর্ম্মা বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। একদিন তাঁহার রাজপ্রাসাদে একটি শকুনি পতিত হওয়ায় শান্তি যজ্ঞের অনুষ্ঠান আবশ্যক হইল। গৌড়ের ব্রাহ্মণগণ নিরগ্নিক ও যজ্ঞে অনভিজ্ঞ, সুতরাং রাজা শ্যামলবর্ম্মা তাঁহার শ্বশুর কান্যকুজের (মতান্তরে কাশীর) রাজা নীলকণ্ঠের নিকট গমন করিয়া তথা হইতে যশোধর মিশ্র ও অন্য চারিজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া ১০০১ শাকে (১০৭৯ অব্দে) স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। যজ্ঞ সমাপনান্তে শ্যামলবর্ম্মা গ্রামাদি দান করিয়া তাহাদিগকে এই দেশে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তাঁহাদের সন্তানেরাই পাশ্চাত্য বৈদিক নামে খ্যাত হইয়াছেন।”
পূর্ব্বোক্ত রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের কুলগ্রন্থের ন্যায় উল্লিখিত বিবরণের প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই বৈদিক কুলজী গ্রন্থে পরস্পরবিরোধী মত পাওয় যায়। এমনকি কোনো কোনো কুলগ্রন্থে রাজার নাম শ্যামলবর্ম্মার পরিবর্তে হরিবর্ম্মা বলিয়া লিখিত হইয়াছে। অবশ্য এই দুইজনই বৰ্ম্মবংশীয় প্রসিদ্ধ রাজা। কোনো কোনো কুলগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে শ্যামলবর্ম্মা কর্ত্তৃক আনীত পঞ্চ গোত্রীয় বৈদিক ব্রাহ্মণেরা কালক্রমে ‘বেদজ্ঞান-বিমূঢ় হওয়াতে ১১০২ শকাব্দে অন্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা আসিয়া বৈদিক কুলে মিলিত হন। সুতরাং এই সমুদয় মতামতের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে।
বাংলায় গ্রহ-বিপ্র নামে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছেন। ইঁহারা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বলিয়াও পরিচিত। ইঁহাদের কুলপঞ্জিকায় উক্ত হইয়াছে যে গৌড়ের রাজা শশাঙ্ক রোগাক্রান্ত হইয়া বৈদ্যগণের চিকিৎসায় সুফল না পাওয়ায় সরযূ নদীর তীরবাসী জপ-যজ্ঞপরায়ণ দ্বাদশ জন ব্রাহ্মণকে আনাইয়া গ্ৰহযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন ও রোগমুক্ত হন। রাজার আদেশে ইঁহারা সপরিবারে গৌড়দেশে বাস করেন। ইঁহারা শাকদ্বীপবাসী মার্তণ্ডাদি আটজন মুনির বংশধর। গরুড় শাকদ্বীপ হইতে ইহাদের পূৰ্বপুরুষগণকে মধ্যদেশে আনয়ন করিয়াছিলেন।
এতদ্ব্যতীত অন্য কোনো কোনো শ্রেণীর ব্রাহ্মণও সম্ভবত হিন্দু যুগে বাংলায় ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। বল্লালসেন তাঁহার গুরু অনিরুদ্ধভট্ট সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে অনুমিত হয় যে তিনি সারস্বত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। কুলজী অনুসারে অন্ধরাজ শূদ্রক সরস্বতী নদীর তীর হইতে তাঁহাদিগকে আনয়ন করেন। কুলজী গ্রন্থে ব্যাস, পরাশর, কৌণ্ডিণ্য, সপ্তশতী প্রভৃতি অন্য যে সমুদয়, ব্রাহ্মণশ্রেণীর উল্লেখ আছে তাঁহার কোনোটিই যে প্রাচীন হিন্দু যুগে বাংলায় বিদ্যমান ছিল, ইহার বিশ্বস্ত প্রমাণ এখন পৰ্য্যন্তও পাওয়া যায় নাই।
ব্রাহ্মণগণ যে সমাজে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মৰ্যাদা লাভ করিতেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে প্রকৃত ব্রাহ্মণের উচ্চ আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপন করিতেন সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। তাহাদের পাণ্ডিত্য, চরিত্র, ও অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা সমাজের আদর্শ ছিল। কিন্তু সকল ব্রাহ্মণই যে এইরূপ আদর্শ অনুসারে চলিতেন এরূপ মনে করা ভুল। এমনকি শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের যে সমুদয় নির্দিষ্ট কৰ্ম্ম আছে, অনেক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণও তাহা মানিয়া চলেন নাই। ভবদেবভট্ট ও দর্ভপানি বংশানুক্রমিক রাজমন্ত্রী ছিলেন। সমতটে দুইটি ব্রাহ্মণ বংশ সপ্তম শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন। ব্রাহ্মণেরা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ব্রাহ্মণেরা যে অন্য নানাবিধ বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন শাস্ত্রে তাঁহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহার কোনো কোনোটি-যেমন কৃষিকার্য্যে-অনুমোদিত ছিল। কিন্তু অনেকগুলিই নিন্দনীয় ছিল এবং তাঁহার জন্য ব্রাহ্মণগণকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। ভবদেবভট্ট এইরূপ কার্য্যের এক সুদীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন। শূদ্রের অধ্যাপনা ও যাজন ইহার অন্যতম। তৎকালে জাতিভেদের কুফল ও সমাজের অধঃপতন কত দূর পৌঁছিয়াছিল ইহা হইতে তাহা জানা যায়। ভবদেবভট্ট রাজার মন্ত্রীত্ব ও যুদ্ধ করিয়াও ব্রাহ্মণের সর্বোচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের আদর্শ বৃত্তি অধ্যাপন ও যাজন অবলম্বন করিয়া কোনো ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রের জ্ঞান লাভে ও ধৰ্ম্মকাৰ্য্যে সহায়তা করিত তবে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হইত। অর্থাৎ ধৰ্ম্ম ও জ্ঞান লাভের জন্য ব্রাহ্মণের উপদেশ যাহাদের সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন, তাহাদিগকে সাহায্য করা ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দনীয় ছিল। চিত্রাদি শিল্প, বৈদ্যক ও জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতির চর্চ্চাও ব্রাহ্মণগণের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু রাজ্যশাসন, যুদ্ধ করা প্রভৃতি ব্রাহ্মণের আদর্শের সম্পূর্ণ বিরোধী কাজ করিয়াও ভবদেবের ন্যায় ব্রাহ্মণগণ আত্মশ্লাঘা করিতেন। ব্রাহ্মণগণের এই মনোবৃত্তিই যে সামাজিক অবনতি ও জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুন্নতির একটি প্রধান কারণ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।
.
৩. করণ-কায়স্থ
প্রাচীন বঙ্গসমাজে ব্রাহ্মণের পরেই সম্ভবত করণ জাতির প্রাধান্য ছিল। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে সংকর জাতির মধ্যে প্রথমেই করণের উল্লেখ আছে। করণগণ যে খুব উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁহারও প্রমাণ আছে। সামন্ত রাজা লোকনাথ করণ ছিলেন এবং বৈন্যগুপ্তের তাম্রশাসনে একজন করণ কায়স্থ সান্ধিবিগ্রহিক বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। শব্দ-প্রদীপ নামক একখানি বৈদ্যক গ্রন্থের প্রণেতা নিজেকে করণায় বলিয়াছেন। তিনি নিজে রাজবৈদ্য ছিলেন এবং তাঁহার পিতা ও পিতামহ রামপাল ও গোবিন্দচন্দ্রের রাজবৈদ্য ছিলেন। রামচরিত-প্রণেতা সন্ধ্যাকর নন্দীর পিতা সান্ধিবিগ্রহিক ও করণাগুণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।
প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে করণ শব্দে একটি জাতি ও এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী (লেখক, হিসাবরক্ষক প্রভৃতি) বুঝায়। কায়স্থ শব্দও প্রথমে এই শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারী বুঝাইত, পরে জাতিবাচক সংজ্ঞায় পরিণত হয়। কোষকার বৈজয়ন্তী কায়স্থ ও করণ প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। প্রাচীন লিপিতেও করণ ও কায়স্থ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। করণজাতি হিন্দু যুগের পরে ক্রমে বঙ্গদেশে লোপ পাইয়াছে, আবার কায়স্থ জাতি হিন্দু যুগের পূর্ব্বে এদেশে সুপরিচিত ছিল না, পরে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। সুতরাং এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, ভারতবর্ষের অন্য কোনো কোনো প্রদেশের ন্যায় বাংলা দেশেও করণ কায়স্থে পরিণত হইয়াছে অর্থাৎ উভয়ে মিলিয়া এক জাতিতে পরিণত হইয়াছে।
খৃষ্টীয় পঞ্চম, ষষ্ঠ ও অষ্টম শতাব্দীর তাম্রশাসনে ‘প্রথম-কায়স্থ’ ও ‘জ্যেষ্ঠকায়স্থ প্রভৃতির উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে তখনো বাংলায় কায়স্থ শব্দে এক শ্রেণীর রাজকর্ম্মচারী মাত্র বুঝাইত। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর একখানি শিলালিপিতে গৌড় কায়স্থ বংশের উল্লেখ আছে। সুতরাং এই সময়ে বাংলায় কায়স্থ জাতির উৎপত্তি হইয়াছে এরূপ মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে বৃহদ্ধর্ম্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কায়স্থের কোনো উল্লেখ নাই। কুলজী গ্রন্থের মতে আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে যে পঞ্চ ভৃত্য আসিয়াছিল তাহারাই ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, দত্ত প্রভৃতি কুলীন কায়স্থের আদিপুরুষ।
.
৪. অনুষ্ঠ-বৈদ্য
বৈদ্য শব্দে প্রথমে চিকিৎসক মাত্র বুঝাইত-পরে ইহা একটি জাতিবাচক সংজ্ঞায় পরিণত হইয়াছে। ঠিক কোন সময়ে বাংলা দেশে এই জাতির প্রতিষ্ঠা হয় তাহা বলা কঠিন। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর চারিখানি লিপিতে দক্ষিণ ভারতবর্ষে বৈদ্যজাতির উল্লেখ আছে। ইঁহারা রাজ্যে ও সমাজে উচ্চমৰ্য্যাদার অধিকারী ছিলেন এবং হঁহাদের কেহ কেহ ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচিত হইতেন। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দের পূৰ্ব্বে বাংলায় বৈদ্যজাতির অস্তিত্বের কোনো বিশ্বস্ত প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। শ্রীহট্টের রাজা ঈশানদেবের তাম্রশাসনে তাঁহার মন্ত্রী (পউনিক) বনমালীকর বৈদ্যবংশপ্রদীপ’ বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলার তিনজন রাজার রাজবৈদ্য করণবংশীয় ছিলেন। সুতরাং হিন্দু যুগে বাংলার চিকিৎসা-ব্যবসায়ীরা যে বৈদ্য নামক বিশিষ্ট কোনো জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতেন ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।
প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে অন্বষ্ঠ জাতির উল্লেখ আছে। মনুসংহিতা অনুসারে চিকিৎসা ইহাদের বৃত্তি। মধ্যযুগে বাংলা দেশে অন্বষ্ঠ বৈদ্যজাতির অপর নাম বলিয়া গৃহীত হইত। বর্ত্তমানকালে অনেক বৈদ্য ইহা স্বীকার করেন না, কিন্তু সুপ্রসিদ্ধ। ভরতমল্লিক অনুষ্ঠ ও বৈদ্য বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে অনুষ্ঠ ও বৈদ্য একই জাতির নাম, কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অনুসারে এ দুইটি ভিন্ন জাতি। সম্ভবত বাংলায় বৈদ্য ও অনুষ্ঠ, কায়স্থ ও করণের ন্যায় একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। বিহার ও যুক্তপ্রদেশে অনেক কায়স্থ অন্বষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেন। সূতসংহিতায় অন্বষ্ঠকে মাহিষ্য বলা হইয়াছে, কিন্তু ভরতমল্লিক বৈদ্য ও অন্যষ্ঠের অভিন্নত্ব-সূচক ব্যাস, অগ্নিবেশ ও শঙ্খস্মৃতি হইতে তিনটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার কোনো স্মৃতিই খুব প্রাচীন নহে, এবং শ্লোকগুলিও অকৃত্রিম কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।
.
৫. অন্যান্য জাতি
বাংলার অন্যান্য জাতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। যুগী, সুবর্ণবণিক ও কৈবর্ত্ত জাতি সম্বন্ধে বল্লালচরিতে অনেক কথা আছে, কিন্তু এই সমুদয় কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য নহে। রামপালের প্রসঙ্গে দিব্য নামক কৈবৰ্ত্তনায়কের বিদ্রোহের উল্লেখ করা হইয়াছে। দিব্য, রুদোক ও ভীম এই তিনজন কৈবর্ত্ত রাজা বরেন্দ্রে রাজত্ব করেন, সুতরাং রাজ্যে ও সমাজে কৈবর্ত্ত জাতির যে বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু সমসাময়িক স্মাৰ্ত্ত পণ্ডিত ভবদেবভট্ট কৈবৰ্ত্তকে অন্ত্যজ জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কৈবর্ত্ত ও মাহিষ্য সম্ভবত একই জাতি, কারণ উভয়েই স্মৃতি ও পুরাণে ক্ষত্রিয় পিতা ও বৈশ্যা মাতার সন্তান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে পূর্ব্ববঙ্গের মাহিষ্য এবং পশ্চিমবঙ্গের চাষী কৈবৰ্ত্ত এক জাতি বলিয়া পরিগণিত। ইঁহাদের মধ্যে অনেক জমিদার ও তালুকদার আছেন এবং মেদিনীপুর জিলায় হঁহারাই খুব সম্ভ্রান্ত শ্ৰেণী। কিন্তু আর এক শ্রেণীর কৈবর্ত্ত ধীবর বলিয়া পরিচিত এবং মৎস্য বিক্রয়ই ইহাদের ব্যবসায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে তীবর-সংসর্গহেতু কলিযুগে কৈবৰ্তগণ পতিত হইয়া ধীবরে পরিণত হইয়াছে। সম্ভবত বর্ত্তমানকালের ন্যায় প্রাচীনকালেও কৈবর্ত্ত জাতি হালিক ও জালিক এই দুই বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। বিষ্ণুপুরাণে যে কৈর্বত্ত জাতিকে অব্ৰহ্মণ্য বলা হইয়াছে, এবং বল্লালসেন যে কৈবৰ্ত্ত জাতিকে জলাচরণীয় করিয়াছিলেন বলিয়া বল্লালচরিতে উক্ত হইয়াছে, তাহা সম্ভবত কেবলমাত্র শেষোক্ত শ্ৰেণী সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। বাংলার আরও অনেক জাতির মধ্যে এইরূপ উচ্চ ও নীচ শ্ৰেণী দেখিতে পাওয়া যায়। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে উত্তম সংকর শ্ৰেণীর মধ্যে গোপের উল্লেখ আছে, ইহারা লেখক; কিন্তু মধ্যম সংকরের মধ্যে আভীর জাতির উল্লেখ আছে, ইহারা সম্ভবত দুগ্ধ-ব্যবসায়ী। বর্ত্তমানকালেও সপোপ ও গয়লা দুইটি বিভিন্ন জাতি।
বৃহদ্ধর্ম্ম ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে যে সমুদয় নীচ জাতির উল্লেখ আছে তাঁহার প্রায় সকলগুলিই বর্ত্তমানকালে সুপরিচিত। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে ইহাদিগকে বর্ণাশ্রম-বহিষ্কৃত ও অন্ত্যজ বলা হইয়াছে। ভবদেবভট্টের মতে রজক, চর্মকার, নট, বরুড় কৈবর্ত্ত, মদে ও ভিল্ল এই সাতটি অন্ত্যজ জাতি। কিন্তু বৃহদ্ধর্ম্ম অনুসারে রজক ও নট মধ্যম সংকর জাতীয় এবং ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মতে ভিল্ল সৎশূদ্র। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে স্থান ও কাল অনুসারে সমাজে বিভিন্ন জাতির উন্নতি ও অবনতি হইয়াছে।
প্রাচীন বৌদ্ধ চর্যাপদে ডোম, চণ্ডাল, ও শবরের কিছু কিছু বিবরণ আছে। ডোমেরা শহরের বাহিরে বাস করিত এবং অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য হইত। তাহারা বাঁশের ঝুড়ি বানাইত ও তাঁত বুনিত। ডোম মেয়েদের স্বভাব-চরিত্র ভালো ছিল না; তাহারা নাচিয়া-গাহিয়া বেড়াইত। চণ্ডালেরা মাঝে মাঝে গৃহস্থের বধূ চুরি করিয়া নিত। শবরেরা পাহাড়ে বাস করিত। তাহাদের মেয়েরা কানে দুল এবং ময়ূরপুচ্ছ ও গুঞ্জাফলের মালা পরিত। নৈহাটি তাম্রশাসনে পুলিন্দ নামে আর এক শ্রেণীর আদিম জাতির উল্লেখ আছে। তাহারা বনে বাস করিত, এবং তাহাদের মেয়েরাও গুঞ্জাফলের মালা পরিত। শবর জাতির কথা প্রাচীন বাংলার অন্য গ্রন্থেও আছে। সম্ভবত পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রে যে কয়েকটি আদিম অসভ্য নর-নারীর মূৰ্ত্তি আছে তাহারা শবর অথবা পুলিন্দজাতীয়। ইহাদের মধ্যে নর-নারী উভয়েরই কটিদেশে কয়েকটি বৃক্ষপত্র ব্যতীত আর কোনো আবরণ নাই। মেয়েরা কিন্তু পরিপাটি করিয়া কেশ-বিন্যাস করিত এবং পত্রপুষ্পের অনেক অলঙ্কার পরিত। পুরুষ ও স্ত্রীলোক উভয়েই বেশ সবলকায় ছিল এবং তীর-ধনুক ও খড়গ ব্যবহার করিতে জানিত। একটি উৎকীর্ণ ফলকে দেখা যায় একজন স্ত্রীলোক একটি মৃত জন্তু হাতে ঝুলাইয়া বীরদর্পে চলিয়াছে,-সম্ভবত নিজেই ইহা শিকার করিয়া আনিয়াছে, এবং ইহাই তাহাদের প্রধান খাদ্য ছিল। বাংলা দেশে সৰ্ব্বপ্রাচীনকালে যে সমুদয় জাতি বাস করিত সম্ভবত ইহারা তাহাদেরই বংশধর, এবং সহস্রাধিক বৎসরেও ইহাদের জীবনযাত্রার বিশেষ কোনো পরিবর্ত্তন হয় নাই।
.
৬. পূজা-পার্ব্বণ এবং আমোদ-উৎসব
দেব-দেবীর পূজা ব্যতীত ধর্ম্মের অনেক লৌকিক অনুষ্ঠানও প্রাচীনকালের সামাজিক জীবনে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিত। ধর্ম্মশাস্ত্রে বহুবিধ সংস্কারের উল্লেখ আছে,-জন্মের পূৰ্ব্ব হইতে মৃত্যুর পর পর্য্যন্ত মানুষের বিভিন্ন অবস্থায় এইগুলি পালনীয়। শিশুর জন্মের পূর্ব্বেই তাঁহার মঙ্গলের জন্য গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন ও শোষ্যন্তী-হোম অনুষ্ঠিত হইত। জন্মের পর জাতকৰ্ম্ম, নিষ্ক্রমণ, নামকরণ, পৌষ্টককৰ্ম্ম, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ ও উপনয়ন। তাঁহার পর ছাত্রজীবনের আরম্ভ। শিক্ষা সমাপ্ত হইলে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সমাবর্ত্তন উৎসব; তৎপর বিবাহ ও নূতন গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে শালাকৰ্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে হইত। মৃত্যুর অব্যবহিত পূৰ্ব্বে ও পরে নানাবিধ ঔদ্ধদৈহিক ক্রিয়ার ব্যবস্থা ছিল এবং অশৌচ পালন ও শ্রাদ্ধাদি শাস্ত্রের নিয়ম অনুসারেই আচরিত হইত। বাংলার স্মার্ত পণ্ডিতেরা এই সমুদয়ের যে বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে মনে হয় যে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার সহিত বাংলার এই বিষয়ে বিশেষ কোনো অনৈক্য ছিল না, এবং লোকাঁচারের যে প্রভেদ ছিল বর্ত্তমানকালেও তাঁহার প্রায় সবই বর্ত্তমান। এই সমুদয় সংস্কার ছাড়াও বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রবল প্রভাব ছিল। কোন কোন তিথিতে কী কী খাদ্য ও কর্ম্ম নিষিদ্ধ, কোন তিথিতে উপবাস করিতে হইবে, এবং অধ্যয়ন, বিদেশযাত্রা, তীর্থগমন প্রভৃতির জন্য কোন কোন কাল শুভ বা অশুভ ইত্যাদি বিষয়ে শাস্ত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশাসন দ্বারা প্রত্যেকের জীবন কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হইত। কিন্তু তাই বলিয়া সেকালের জীবন একেবারে নিরানন্দ বা বৈচিত্র্যহীন ছিল না। বিবাহাদি উপলক্ষে নৃত্যগীতাদি আমোদ-উৎসব হইত। চর্যাপদে উক্ত হইয়াছে যে, বর বিবাহ করিতে যাইবার সময় পটহ, মাদল, করৎ, কলা, দুন্দুভি প্রভৃতির বাদ্য হইত। ইহা ছাড়া তখনো বাংলায় বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ হইত এবং এই সমুদয় পূজা পাৰ্বণ প্রভৃতি উপলক্ষে নানাবিধ আমোদ-উৎসব অনুষ্ঠিত হইত।
এখানকার ন্যায় প্রাচীন হিন্দু যুগেও দুর্গাপূজাই বাংলার প্রধান পৰ্ব ছিল। সন্ধ্যাকরনন্দী রামচরিতে লিখিয়াছেন যে উমা অর্থাৎ দুর্গার অর্চনা উপলক্ষে বরেন্দ্রে বিপুল উৎসব হইত। অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থেও এই উৎসবের বিবরণ আছে। শারদীয় দুর্গাপূজায় বিজয়া দশমীর দিন শাবরোৎসব’ নামে এক প্রকার নৃত্য গীতির অনুষ্ঠান হইত। শবরজাতির ন্যায় কেবলমাত্র বৃক্ষপত্র পরিধান করিয়া এবং সারা গায়ে কাদা মাখিয়া, ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে লোকেরা অশ্লীল গান গাহিত এবং তদনুরূপ কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী করিত। জীমূতবাহন কাল-বিবেক’ গ্রন্থে যে ভাষায় এই নৃত্যগীতের বর্ণনা করিয়াছেন বর্ত্তমানকালের রুচি অনুসারে তাঁহার উল্লেখ বা ইঙ্গিত করাও অসম্ভব। অথচ তিনিই লিখিয়াছেন যে, যে ইহা না করিবে ভগবতী ক্রুদ্ধা হইয়া তাহাকে নিদারুণ শাপ দিবেন। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে কতিপয় অশ্লীল শব্দ সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে ইহা অপরের সম্মুখে উচ্চারণ করা কর্তব্য নহে, কিন্তু আশ্বিন মাসে মহাপূজার দিনে ইহা উচ্চারণ করিবে,-তবে মাতা, ভগিনী এবং শক্তিমন্ত্রে অদীক্ষিতা শিষ্যার সম্মুখে নহে। ইহার সপক্ষে এই পুরাণে যে যুক্তি দেওয়া হইয়াছে, শ্লীলতা বজায় রাখিয়া তাঁহার উল্লেখ করা যায় না। ধর্ম্মের নামে এই সমুদয় বীভৎসতা যে অনেক পরিমাণে তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের ফল তাহা অস্বীকার করা কঠিন। উপযুক্ত অধিকারীর পক্ষে এই সমুদয় অনুষ্ঠান প্রয়োজনীয় অথবা ফলপ্রদ হইতে পারে, তর্কের খাতিরে ইহা স্বীকার করিলেও সৰ্ব্বসাধারণের উপর ইহার প্রভাব যে নীতি ও রুচির দিক দিয়া অত্যন্ত অশুভ হইয়াছিল, বাংলার সামাজিক ইতিহাস আলোচনা করিলে যে বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না। চৈত্র মাসে কাম মহোৎসবেও বাদ্য-সহকারে এই প্রকার অশ্লীল গীত গান করা হইত, কারণ লোকের বিশ্বাস ছিল যে ইহাতে পরিতুষ্ট হইয়া কামদেব ধন, পুত্র প্রভৃতি দান করিবেন। হোলকা-বৰ্ত্তমান কালের হোলি-একটি প্রধান উৎসব ছিল। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ইহাতে যোগদান করিত, কিন্তু ইহার কোনো বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। দূত-প্রতিপদ নামে একটি বিশেষ উৎসব কার্তিক মাসের শুক্ল প্রতিপদে অনুষ্ঠিত হইত। প্রাতে বাজী রাখিয়া পাশা খেলা হইত, এবং লোকের বিশ্বাস ছিল যে ইহার ফলাফল আগামী বৎসরের শুভাশুভ নির্দেশ করে। তাঁহার পর বসন-ভূষণ পরিধান ও গন্ধ দ্রব্যাদি লেপন করিয়া সকলে গীতবাদ্যে যোগদান করিত এবং বন্ধুবান্ধবসহ ভোজন করিত। রাত্রে শয়নকক্ষ ও শয্যা বিশেষভাবে সজ্জিত হইত এবং প্রণয়ীযুগল একত্রে রাত্রি যাপন করিত। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রেও অক্ষক্রীড়া হইত এবং আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব একত্র হইয়া ভোজন। করিতেন। চিড়া ও নারিকেলের প্রস্তুত নানাবিধ দ্রব্য এই রাত্রে প্রধান খাদ্য ছিল। কার্তিক মাসে সুখরাত্রিব্রত পালিত হইত। সন্ধ্যাকালে গরীব-দুঃখীকে খাওয়ানো হইত এবং পরদিন প্রভাতে যাহার সহিত দেখা হইত, বন্ধু বা আত্মীয় না হইলেও তাহাকে কুশলবচন এবং পুষ্প, গন্ধ, দধি প্রভৃতি দ্বারা অর্চনা করা হইত। ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া, পাষাণ-চতুর্দশীব্রত, আকাশ-প্রদীপ, জন্মাষ্টমী, অক্ষয়-তৃতীয়া, দশহরার গঙ্গাস্নান, অষ্টমীতে ব্রহ্মপুত্র স্নান প্রভৃতি বৰ্ত্তমানকালের সুপরিচিত অনুষ্ঠানগুলিও তকালে প্রচলিত ছিল। সেই যুগে শক্রোখান নামে একটি উৎসব ছিল। ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে ইন্দ্রের কাষ্ঠনির্ম্মিত বিশাল ধ্বজ-দণ্ড উত্তোলন করা হইত। এই উপলক্ষে সুবেশধারী নাগরিকগণ সমবেত হইতেন এবং রাজা স্বয়ং দৈবজ্ঞ, সচিব, কুঞ্চুকী ও ব্রাহ্মণগণ সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়া উৎসবে যোগদান করিতেন। এই জাতীয় উৎসব এখন একেবারেই লোপ পাইয়াছে। এই সমুদয় পূজা-পাৰ্বণ, উৎসব প্রভৃতি ও তদুপলক্ষে আমোদ-প্রমোদ বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল।
.
৭. বাঙ্গালীর চরিত্র ও জীবনযাত্রা
এই যুগে সাধারণ বাঙ্গালীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার কোনো স্পষ্ট বা বিস্তৃত বিবরণ জানিবার উপায় নাই। প্রাচীন বাংলায় লিখিত চর্যাপদগুলিতে এ বিষয়ে কিছু কিছু উল্লেখ আছে। কিন্তু এই পদগুলি দশম শতাব্দী বা তাঁহার পরে রচিত, এবং অন্যান্য যে সমুদয় গ্রন্থে ইহার কোনো বিবরণ আছে তাহা ইহারও পরবর্ত্তীকালের রচনা। প্রাচীন লিপি, শিল্প ও বৈদেশিক ভ্রমণকারীর বিবরণী হইতে এ বিষয়ে যে তথ্য সংগ্রহ করা যায় তাহাও অতিশয় স্বল্প। এই সমুদয়ের উপর নির্ভর করিয়াই বাঙ্গালীর জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিতেছি।
সপ্তম শতাব্দীতে চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন সাং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণ করিয়া ইহার অধিবাসীদের সম্বন্ধে যে সমুদয় মন্তব্য করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালী মাত্রেরই শ্লাঘার বিষয়। ‘সমতটের লোকেরা স্বভাবতই শ্রমসহিষ্ণু, তাম্রলিপ্তির অধিবাসীরা দৃঢ় ও সাহসী কিন্তু চঞ্চল ও ব্যস্তবাগীশ, এবং কর্ণসুবর্ণবাসীরা সাধু ও অমায়িক’-তাঁহার এই কয়েকটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে প্রাচীন বাঙ্গালীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাছাড়া তিনি পুণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট ও কর্ণসুবর্ণে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে লেখাপড়া শিখিবার অদম্য আগ্রহ ও প্রাণপণ চেষ্টার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। সহস্রাধিক বৎসর পরে আজিও ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলায় স্কুল-কলেজের সংখ্যাধিক্য বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতেছে।
বাংলায় সাধারণত বেদ, মীমাংসা, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, অর্থশাস্ত্র গণিত, জ্যোতিষ, কাব্য, তর্ক, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দ, আয়ুর্ব্বেদ, অস্ত্রবেদ, আগম, তন্ত্র প্রভৃতির পঠনপাঠন প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের গ্রন্থাদিও পঠিত হইত। ফাহিয়ান ও ইৎসিং উভয়েই বৌদ্ধ গ্রন্থের চর্চ্চার জন্য তাম্রলিপ্তির বৌদ্ধবিহারে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন।
জ্ঞান লাভের জন্য বাঙ্গালী দূরদেশে এমনকি সুদূর কাশীর পর্য্যন্ত যাইত। কিন্তু বাঙ্গালী ছাত্রদের কোনো কোনো বিষয়ে দুর্নাম ছিল। ক্ষেমেন্দ্র দশোপদেশ নামক হাস্যরসাত্মক কাব্যে লিখিয়াছেন যে গৌড়ের ছাত্রগণ যখন প্রথম কাশ্মীরে আসে তখন তাহাদের ক্ষীণ দেহ দেখিয়া মনে হয় যেন ছুঁইলেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে; কিন্তু এখানকার জলবায়ুর গুণে তাহারা শীঘ্রই এমন উদ্ধত হইয়া উঠে যে, দোকানদার দাম চাহিলে দাম দেয় না, সামান্য উত্তেজনার বশেই মারিবার জন্য ছুরি উঠায়। বিজ্ঞানেশ্বরও লিখিয়াছেন যে গৌড়ের লোকেরা বিবাদপ্রিয়।
কিন্তু বাংলার মেয়েদের সুখ্যাতি ছিল। বাৎস্যায়ন তাহাদিগকে মৃদ্যুভাষিণী, কোমলাঙ্গী ও অনুরাগবতী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পবনদূত বিজয়পুরের বর্ণনা পড়িয়া মনে হয়, সেকালে মেয়েদের মধ্যে অবরোধ-প্রথা ছিল না-তাহারা স্বচ্ছন্দে বাহিরে ভ্রমণ করিত। কিন্তু বাৎস্যায়ন লিখিয়াছেন যে রাজান্তঃপুরের মেয়েরা পর্দার আড়াল হইতে অনাত্মীয় পুরুষের সহিত আলাপ করিত। মেয়েরা লেখাপড়া শিখিত। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশের ন্যায় বাংলায়ও মেয়েদের কোনো প্রকার স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা ছিল না, প্রথমে পিতা পরে স্বামীর পরিবারবর্গের অধীনে থাকিতে হইত। এক বিষয়ে বাংলার বৈশিষ্ট্য ছিল। জীমূতবাহনের মতে অপুত্রক স্বামীর মৃত্যু হইলে বিধবা তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে। এ বিষয়ে প্রাচীনকালে অনেক বিরুদ্ধ মত ছিল, যেমন পুত্রের অভাবে ভ্রাতা উত্তরাধিকারী এবং বিধবা কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের অধিকারিণী হইবে। জীমূতবাহন এই সমুদয় মত খণ্ডন করিয়া বিধবার দাবী সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং বাংলা দেশে এই বিধি প্রচলিত ছিল ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সেকালের বিধবার জীবন এখনকার ন্যায়ই ছিল। কারণ জীমূতবাহনের মতে সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেও ইহার দান ও বিক্রয় সম্বন্ধে বিধবার কোনো অধিকার থাকিবে না, এবং তাহাকে সতী-সাধ্বী স্ত্রীর ন্যায় কেবলমাত্র স্বামীর স্মৃতি বহন করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইবে। স্বামীর পরিবারে সর্ববিষয়ে-এমনকি সম্পত্তির ব্যবস্থা সম্বন্ধেও-তাহাদের আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকিতে হইবে, এবং নিজের প্রাণধারণাৰ্থ যাহা প্রয়োজন, মাত্র তাহা ব্যয় করিয়া অবশিষ্ট স্বামীর পারলৌকিক কল্যাণের সর্ববিধ বিলাস-বর্জন ও কৃচ্ছসাধন করিতে হইত। সধবা অবস্থায় তাঁহার ব্যক্তিগত প্রভাব ও প্রতিপত্তি কিরূপ ছিল ঠিক বলা যায় না। তবে পুরুষের বহু-বিবাহ প্রচলিত ছিল এবং অনেক স্ত্রীকেই সপত্নীর সহিত একত্র জীবন যাপন করিতে হইত। সহমরণ প্রথা সেকালেও প্রচলিত ছিল এবং বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে ইহার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আছে।
বাংলার অধিবাসীরা তখন বেশির ভাগ গ্রামেই বাস করিত। কিন্তু ধন-সম্পদপূর্ণ শহরেরও অভাব ছিল না। রামচরিতে সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা বঙ্গভূমির এবং পাল-রাজধানী রামাবতীর মনোরম বর্ণনা আছে। পবনদূতে সেন রাজধানী বিজয়পুরের বিবরণ পাওয়া যায়। অত্যুক্তিদোষে দূষিত হইলেও এই সমুদয় বর্ণনা হইতে সেকালের গ্রাম্য ও নাগরিক জীবনের কিছু আভাস পাওয়া যায়।
রামাবতী বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি লিখিয়াছেন যে প্রশস্ত রাজপথের ধারে কনক পরিপূর্ণ ধবল প্রাসাদ-শ্ৰেণী মেরু-শিকরের ন্যায় প্রতীয়মান ইহত এবং ইহার উপর স্বর্ণকলস শোভা পাইত; নানা স্থানে মন্দির, স্তূপ, বিহার, উদ্যান, পুষ্করিণী, ক্রীড়াশৈল, ক্রীড়াবাপী ও নানাবিধ পুষ্প, লতা, তরু, গুল্ম নগরের শোভাবৃদ্ধি করিত। হীরক, বৈদুৰ্য্যমণি, মুক্তা, মরকত, মানিক্য ও নীলমণিখচিত আভরণ, বহুবিধ স্বর্ণখচিত তৈজসপত্র ও অন্যান্য গৃহোপকরণ, মহামূল্য বিচিত্র, সূক্ষ্ম বসন, কস্তুরী, কালাগুরু, চন্দন, কুঙ্কুম ও কপূরাদি গন্ধদ্রব্য, এবং নানা যন্ত্রোখিত মন্দ্রমধুর ধ্বনির সহিত তানলয়-বিশুদ্ধ সঙ্গীত সেকালের নাগরিকদের ঐশ্বর্য, সম্পদ, রুচি ও বিলাসিতার পরিচয় প্রদান করিত। সন্ধ্যাকরনন্দী স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে, সেকালে সমাজে ব্যভিচারী ও সাত্ত্বিক উভয় শ্রেণীর লোক ছিল। নগরে বিলাসিতা ও উজ্জ্বলতা অবশ্য গ্রামের তুলনায় বেশী মাত্রায়ই ছিল।
বাংলার প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে নৈতিক জীবনের খুব উচ্চ আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে সত্য, শৌচ, দয়া, দান প্রভৃতি সর্ব্ববিধগুণের মহিমা কীর্তন এবং অপরদিকে ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য ও পরদারগমন প্রভৃতি মহাপাতক বলিয়া গণ্য করিয়া তাঁহার জন্য কঠোর শাস্তি ও গুরুতর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনে এই আদর্শ কী পরিমাণে অনুসৃত হইত তাঁহার সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যায় না। সামাজিক জীবনের কিছু কিছু দুর্নীতি ও অশ্লীলতার কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয় সংযম বা দৈহিক পবিত্রতার আদর্শ যে হিন্দু যুগের অবসানকালে অনেক পরিমাণে খৰ্ব্ব হইয়াছিল এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই যুগের কাব্যে ইন্দ্রিয়ের উচ্ছলতা যেভাবে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে তাহা কেবলমাত্র কবির কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। যে যুগের স্মার্ত পণ্ডিতগণ প্রামাণিক গ্রন্থে অকুণ্ঠিত চিত্তে লিখিয়াছেন যে শূদ্রাকে বিবাহ করা অসঙ্গত কিন্তু তাঁহার সহিত অবৈধ সহবাস করা তাদৃশ নিন্দনীয় নয়; যে যুগের কবি রাজপ্রশস্তিতে রাজার কৃতিত্বের নিদর্শনস্বরূপ গৰ্ব্বভরে বলিয়াছেন যে রাজপ্রাসাদে (অথবা রাজধানীতে) প্রতি সন্ধ্যায় ‘বেশবিলাসিনীজনের মঞ্জীর মঙুস্বনে’ আকাশ প্রতিধ্বনিত হয়; যে যুগের কবি মন্দিরের একশত দেবদাসীর রূপ-যৌবন বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া লিখিয়াছেন যে, ইহারা ‘কামিজনের কারাগার ও সঙ্গীত-কেলি-শ্রীর সঙ্গমগৃহ’ এবং ইহাদের দৃষ্টিমাত্রে ভস্মীভূত কাম পুনরুজ্জীবিত হয়; যে যুগের কবি বিষ্ণুমন্দিরে লীলাকমলহস্তে দেবদাসীগণকে লক্ষ্মীর সহিত তুলনা করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই; সে যুগের নর-নারীর যৌন সম্বন্ধের ধারণা ও আদর্শ বর্ত্তমানকালের মাপকাঠিতে বিচার করিলে খুব উচ্চ ও মহৎ ছিল এরূপ বিশ্বাস করা কঠিন। এ বিষয়ে পূৰ্ব্বেও বাঙ্গালীর যে খুব সুনাম ছিল না, তাঁহারও কিছু কিছু প্রমাণ আছে। বাৎস্যায়ন গৌড় ও বঙ্গের রাজান্ত :পুরবাসিনীদের ব্যভিচারের উল্লেখ করিয়াছেন। বৃহস্পতি ভারতের বিভিন্ন জনপদের আচার-ব্যবহার বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, পূৰ্ব্বদেশের দ্বিজাতিগণ মৎস্যাহারী এবং তাহাদের স্ত্রীগণ দুর্নীতিপরায়ণ।
ভাত, মাছ, মাংস, শাকসজী, ফলমূল, দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত নানাপ্রকারের দ্রব্য (ক্ষীর, দধি, ঘৃত ইত্যাদি) বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য ছিল। বাংলার বাহিরে ব্রাহ্মণেরা সাধারণত মাছ-মাংস খাইতেন না এবং ইহা নিন্দনীয় মনে করিতেন। কিন্তু বাংলায় ব্রাহ্মণেরা আমিষ ভোজন করিতেন, এবং ভবদেবভট্ট নানাবিধ যুক্তি প্রয়োগে ইহার সমর্থন করিয়াছেন। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে রোহিত, সকুল, শফর এবং অন্যান্য শ্বেত ও শল্কমুক্ত মৎস্যভক্ষণের ব্যবস্থা আছে। সেকালে ইলিশ মৎস্য এবং পূৰ্ব্ববঙ্গে শুটকী মৎস্যের খুব আদর ছিল। নানারূপ মাদক পানীয় ব্যবহৃত হইত। ভবদেবভট্টের মতে সুরাপান সকলের পক্ষেই নিষিদ্ধ, কিন্তু এই ব্যবস্থা কত দূর কাৰ্য্যকরী ছিল বলা কঠিন। চর্য্যাপদে শৌণ্ডিকালয়ের উল্লেখ আছে।
পাহাড়পুরের মূর্ত্তিগুলি দেখিলে মনে হয় যে, সেকালের বাঙ্গালী নর-নারী সাধারণত এখনকার মতোই একখানা ধুতি ও শাড়ী পরিত। পুরুষেরা মালকোছা দিয়া খাটো ধুতি পরিত এবং অধিকাংশ সময়ই ইহা হাঁটুর নিচে নামিত না। কিন্তু মেয়েদের শাড়ী পায়ের গোড়ালি পর্য্যন্ত পৌঁছাত। ধুতি ও শাড়ি কেবল দেহের নিম্নাদ্ধা আবৃত করিত। নাভির উপরের অংশ কখনো খোলা থাকিত, কখনো পুরুষেরা উত্তরীয় এবং মেয়েরা ওড়না ব্যবহার করিত। মেয়েরা কদাচিৎ চৌলি বা স্তনপট্ট এবং বডিসের ন্যায় জামাও ব্যবহার করিত। উৎসবে বা বিশেষ উপলক্ষে সম্ভবত বিশেষ পরিচ্ছদের ব্যবস্থা ছিল।
পুরুষ ও মেয়েরা উভয়েই অঙ্গুরী, কানে কুণ্ডল, গলায় হার, হাতে কেয়ুর ও বলয়, কটিদেশে মেখলা ও পায়ে মল পরিত। শঙ্খ-বলয় কেবল মেয়েরাই ব্যবহার করিত। পুরুষ ও মেয়ে উভয়েই একাধিক হার গলায় দিত এবং মেয়েরা অনেক সময় এখনকার পশ্চিমদেশীয় স্ত্রীলোকের ন্যায় হাতে অনেকগুলি চুড়িবালা পরিত। ধনীরা সোনা, রূপা, মণি, মুক্তার অনেক আভরণ ব্যবহার করিত।
পুরুষ বা স্ত্রী কেহই কোনোরূপ শিরোভূষণ ব্যবহার করিত না। কিন্তু উভয়ের সুদীর্ঘ কুঞ্চিত কেশদাম নিপুণ কৌশলে বিন্যস্ত হইত। পুরুষদের চুল বাবরির ন্যায় কাঁধের উপর ঝুলিয়া পড়িত, মেয়েরা নানা রকম খোঁপা বাঁধিত।
সেকালের সাহিত্যে চামড়ার জুতা, কাঠের খড়ম এবং ছাতার উল্লেখ আছে। বাংলার প্রস্তুরমূর্ত্তিতে কেবল যোদ্ধাদের পায়ে কখনো কখনো জুতা দেখা যায়। সম্ভবত ইহা সাধারণত ব্যবহৃত হইত না। কয়েকটি মূর্ত্তিতে ছাতার ব্যবহার দেখা যায়।
মেয়েরা বিবাহ হইলে কপালে সিন্দুর পরিত। তাছাড়া চরণদ্বয় অলক্তক, ও নিম্নাধর সিন্দুর দ্বারা রঞ্জিত করিত। কুঙ্কুমাদি নানা গন্ধ দ্রব্যের ব্যবহার ছিল।
সেকালে নানাবিধ ক্রীড়াকৌতুক ছিল। পাশা ও দাবা খেলা এবং নৃত্য-গীত অভিনয়ের খুব প্রচলন ছিল। চৰ্য্যাপদে নানাবিধ বাদ্যযন্ত্রের নাম আছে। পাহাড়পুরের খোদিত ফলকে নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ, করতাল, ঢাক-ঢোল প্রভৃতি তো ছিলই, এমনকি মাটির ভাণ্ডও বাদ্যযন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইত। পুরুষেরা শিকার, মল্লযুদ্ধ, ব্যায়াম ও নানাবিধ বাজীকরের খেলা করিত। মেয়েরা উদ্যান-রচনা, জলক্রীড়া প্রভৃতি ভালোবাসিত।
গরুর গাড়ি ও নৌকাস্থল ও জলপথের প্রধান যানবাহন ছিল। ধনী লোকেরা হস্তী, অশ্ব, রথ, অশ্ব-শকট প্রভৃতি ব্যবহার করিত। বিবাহের পর বর গরুর গাড়ীতে বধূকে লইয়া বাড়ী ফিরিতেন। গরুর গাড়ী কিংশুক ও শাল্মলী কাষ্ঠে নির্ম্মিত হইত। গ্রামের লোকেরা ভেলা ব্যবহার করিত।
১৯. অর্থনৈতিক অবস্থা
১৯. ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ – অর্থনৈতিক অবস্থা
১. কৃষি
বাংলা চিরকালই কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের লোকেরা বেশীর ভাগ গ্রামে বাস করিত এবং গ্রামের চতুস্পার্শ্বস্থ জমি চাষ করিয়া নানা শস্য ও ফলাদি উৎপাদন করিত। এখনকার ন্যায় তখনো ধান্যই প্রধান শস্য ছিল, এবং ইহার চাষের প্রণালীও বর্ত্তমানকালের ন্যায়ই ছিল। খুব প্রাচীনকাল হইতেই এখানে ইক্ষুর চাষ হইত। ইক্ষুর রস হইতে প্রচুর পরিমাণে চিনি ও গুড় প্রস্তুত হইত এবং বিদেশে চালান হইত। কেহ কেহ এরূপও অনুমান করিয়াছেন যে, অধিক পরিমাণে গুড় হইত বলিয়াই এদেশের নাম হইয়াছিল গৌড়। তুলা ও সর্ষপের চাষও এখানে বহুল পরিমাণে হইত। পানের বরজও অনেক ছিল। বহু ফলবান বৃক্ষের রীতিমতো চাষ হইত। ইহার মধ্যে নারিকেল, সুপারি, আম, কাঁঠাল, ডালিম, কলা, লেবু, ডুমুর প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
যাহারা চাষ করিত জমিতে তাহাদের স্বত্ব কিরূপ ছিল, রাজা অথবা জমিদারকে কী হারে খাজনা দিতে হইত, ইত্যাদি বিষয়ে কোনো সঠিক বিবরণ জানা যায় না। সম্ভবত রাজাই দেশের সমস্ত জমির মালিক ছিলেন এবং যাহারা চাষ করিত বা অন্য প্রকারে জমি ভোগ করিত তাহাদের কতকগুলি নির্দিষ্ট কর দিতে হইত। রাজা মন্দির প্রভৃতি ধৰ্ম্ম-প্রতিষ্ঠান এবং ব্রাহ্মণকে প্রতিপালন করিবার জন্য জমি দান করিতেন। এই জমির জন্য কোনো কর দিতে হইত না এবং গ্রহীতা বংশানুক্রমে ইহা চিরকাল ভোগ করিতেন। অনেক সময় ধনীরা রাজদরবার হইতে পতিত জমি কিনিয়া এইরূপ উদ্দেশ্যে দান করিতেন এবং তাহাও নিষ্কর ও চিরস্থায়ী বলিয়া গণ্য হইত।
তখনকার দিনে নল দিয়া জমি মাপ করা হইত। বিভিন্ন সময়ে এবং বিভিন্ন অঞ্চলে নলের দৈর্ঘ্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের ছিল। সমতটীয়-নল এবং বৃষভশঙ্ক নলে’র উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত প্রথমটি সমতট প্রদেশ এবং দ্বিতীয়টি বৃষভশঙ্কর উপাধিধারী সেন-সম্রাট বিজয়সেনের নাম হইতে উদ্ভূত। প্রাচীন গুপ্তযুগে জমির পরিমাণ-সূচক কুল্যবাপ ও দ্রোণবাপ এই দুইটি সংজ্ঞা ব্যবহৃত হইত। কুল্যবাপ শব্দটি কুলা অর্থাৎ কুল্য হইতে উৎপন্ন এবং এক কুলা বীজ দ্বারা যতটুকু জমি বপন করা যায় তাহাকেই সম্ভবত কুল্যবাপ বলা হইত। অবশ্য ক্রমে ইহার একটি পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছিল। কুল্যবাপ শব্দটি এখনো একেবারে লোপ পায় নাই। কাছাড় জিলায় এখনো কুল্যবায় এই মাপ প্রচলিত আছে। ইহা ১৪ বিঘার সমান। কুল্যবায় যে কুল্যবাপেরই রূপান্তর সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রাচীনকালে কুল্যবাপের পরিমাণ কত ছিল তাহা বলা কঠিন। কেহ কেহ মনে করেন যে, ইহা প্রায় তিন বিঘার সমান ছিল। কিন্তু অনেকের বিশ্বাস যে কুল্যবায় ইহার অপেক্ষা অনেক বড় ছিল। কুল্যবাপের আট ভাগের এক ভাগকে দ্রোণবাপ বলা হইত। পরবর্ত্তীকালে কুল্যবাপের পরিবর্তে পাটক অথবা ভূপিটক শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাটক ৪০ দ্রোণের সামন ছিল। এতদ্ব্যতীত আঢ়ক অথবা আঢ়বাপ, উম্মান অথবা উদান এবং কাক অথবা কাকিনিক প্রভৃতি শব্দ জমির পরিমাণ সূচিত করিবার জন্য ব্যবহৃত হইত-কিন্তু ইহার কোনটির কী পরিমাণ ছিল তাহা জানা যায় না।
.
২. শিল্প
বাংলা কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও এখানে নানাবিধ শিল্পজাত দ্রব্য প্রস্তুত হইত। বস্ত্রশিল্পের জন্য এদেশ প্রাচীনকালেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ক্ষৌম, দুকূল, পত্রোণ ও কাঁপাসিক এই চারি প্রকার বস্ত্রের উল্লেখ আছে। ক্ষৌম শণের সূতায় প্রস্তুত মোটা কাপড়; কাশী ও উত্তরবঙ্গে ইহা নির্ম্মিত হইত। এই জাতীয় সূক্ষ্ম কাপড়ের নাম দুকূল। কৌটিল্য লিখিয়াছেন, বঙ্গদেশীয় দুকূল শ্বেত ও স্নিগ্ধ, পুণ্ড্রদেশীয় দুকূল শ্যাম ও মণির ন্যায় স্নিগ্ধ। পত্রোর্ণ রেশমের ন্যায় একজাতীয় কীটের লালায় তৈরী। মগধ ও উত্তরবঙ্গে এই জাতীয় বস্ত্র প্রস্তুত হইত। কাঁপাসিক অর্থাৎ কাঁপাসতুলার কাপড়ের জন্যও বঙ্গ প্রসিদ্ধ ছিল। এইরূপে দেখা যায় যে, খুব প্রাচীনকালেই বাংলার বস্ত্রশিল্প যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দে বাংলা হইতে বহু পরিমাণ উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম বস্ত্র বিদেশে চালান যাইত। বাংলার যে মসলিন ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সমগ্র জগতে বিখ্যাত ছিল, অতি প্রাচীন যুগেই তাঁহার উদ্ভব হইয়াছিল।
প্রস্তর ও ধাতুশিল্প যে এদেশে কত দূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল তাহা শিল্প অধ্যায়ে দেখানো হইয়াছে। মৃৎশিল্পেরও কিছু কিছু পরিচয় পাহাড়পুর প্রভৃতি স্থানের পোড়ামাটির কাজে এবং অসংখ্য তৈজসপত্রে পাওয়া যায়। সেকালে বিলাসিতার উপকরণ যোগাইবার জন্য স্বর্ণকার, মণিকার প্রভৃতির শিল্পও উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কৰ্ম্মকার ও সূত্রধর গৃহ, নৌকা, শকট প্রভৃতি নিৰ্মাণ করিত এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নানা উপকরণ যোগাইত। কাষ্ঠশিল্প যে একটি উচ্চ সূক্ষ্মশিল্পে উন্নীত হইয়াছিল, শিল্প অধ্যায়ে তাঁহার কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। হস্তীদন্তের কাজও আর একটি উচ্চশ্রেণীর শিল্প ছিল।
বাংলার শিল্পীদের সংঘবদ্ধ জীবনের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। নগরশ্রেষ্ঠী, প্রথম-সার্থবাহ, প্রথম-কুলিক প্রভৃতি এইরূপ সংঘের প্রধান ছিলেন ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিজয়সেনের দেওপাড়া লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, রাণক শূলপাণি ‘বারেন্দ্র-শিল্পী-গোষ্ঠী-চূড়ামণি’ ছিলেন। বারেন্দ্রে শিল্পীগণের এই গোষ্ঠী যে এটি বিধিবদ্ধ সংঘ ছিল, এরূপ অনুমান করাই সঙ্গত। এইরূপ সংঘবদ্ধ শিল্পীজীবনের ফলেই বাংলা দেশের নানা শিল্পী ক্রমশ বিভিন্ন বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত হইয়াছে। তন্তুবায়, গন্ধবণিক, স্বর্ণকার, কৰ্ম্মকার, কুম্ভকার, কংসকার, শংখকার, মালাকার, তক্ষক, তৈলকার প্রভৃতি প্রথমে বিভিন্ন শিল্পী-সংঘ মাত্র ছিল, পরে ক্রমে ক্রমে সমাজে এক একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া এক একটি বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছে-সকলেই এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং বাংলার এই সমুদয় জাতিবিভাগ হইতে তৎকালের বিভিন্ন শিল্প, বৃত্তি ও ব্যবসায়ের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।
.
৩. বাণিজ্য
শিল্পের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় বাণিজ্যেরও প্রসার হইয়াছিল। বাংলায় বহু নদ-নদী থাকায় শিল্পজাত দ্রব্যাদি দেশের নানা স্থানে প্রেরণের যথেষ্ট সুবিধা ছিল। এই কারণে বাংলার নানা স্থানে হাট ও গঞ্জ এবং নতুন নতুন নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্থলপথে যাইবার জন্য বড় বড় রাস্তা ছিল এবং প্রাচীন নগরগুলিও বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। হট্টপতি, শৌল্কিক, তরিক প্রভৃতি কর্ম্মচারীদের নাম হইতে বুঝা যায় যে, শিল্প ও বাণিজ্য হইতে রাজ্যের যথেষ্ট আয় হইত।
বাংলার বাণিজ্য কেবল দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। স্থল ও জলপথে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সহিত ইহার দ্রব্যবিনিময় হইত। খুব প্রাচীনকাল হইতেই সমুদ্রপথেও বাংলার বাণিজ্য-ব্যবসায় চলিত। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দে একজন গ্রীক নাবিক লিখিত একখানি গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, গঙ্গা নদীর মোহনায় গঙ্গে নামক বন্দর ছিল,-বণিকেরা সেখান হইতে জাহাজ ছাড়িয়া হয় সমুদ্রের উপকূল ধরিয়া দক্ষিণ ভারত ও লঙ্কাদ্বীপ যাইত, অথবা সোজাসুজি সমুদ্র পাড়ি দিয়া সুবর্ণভূমি অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভতি দেশে যাইত। সূক্ষ্ম মসলিন কাপড়, মুক্তা ও নানা প্রকার গাছগাছড়া এদেশ হইতে চালান যাইত। পরবর্ত্তীকালে তাম্রলিপ্তি-বর্ত্তমান তমলুক-বাংলার প্রধান বন্দর হইয়াছিল। এখান হইতে বাঙ্গালীর জাহাজ দ্রব্যসম্ভার-পরিপূর্ণ হইয়া পৃথিবীর সুদূর প্রদেশে যাইত এবং তথা হইতে ধন ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া ফিরিত।
খৃষ্টপূৰ্ব দ্বিতীয় শতাব্দে অথবা তাঁহার পূর্ব্বে স্থলপথে আসাম ও ব্রহ্মের মধ্য দিয়া বাংলার সহিত চীন আসাম প্রভৃতি দেশের বাণিজ্য-সম্বন্ধ ছিল। দুর্গম হিমালয়ের পথ দিয়াও নেপাল, ভুটান ও তিব্বতের সহিত বাংলার বাণিজ্য চলিত।
এইরূপ শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের ফলে বাংলার ধনসম্পদ ও ঐশ্বৰ্য্য প্রচুর বাড়িয়াছিল।
.
৪. প্রাচীন মুদ্রা
ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় সম্ভবত খৃষ্টজন্মের চারি-পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বেই বাংলায় মুদ্রার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছিল। কারণ ভারতবর্ষের সর্ব প্রাচীন ছাপ-কাটা (Punch marked) মুদ্রা বাংলায় অনেক পাওয়া গিয়াছে, এবং এখানকার সৰ্ব্বপ্রাচীন মৌর্যযুগের লিপিতে মুদ্রার উল্লেখ আছে।
বাংলায় কুষাণযুগের মুদ্রা অল্প কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু গুপ্তযুগের স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা বহু-সংখ্যায় পাওয়া যায়। এই যুগে যে এই সমুদয় মুদ্রার বহুল প্রচলন ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন লিপিতে দীনার ও রূপক এই দুই প্রকার মুদ্রার নাম পাওয়া যায়। সম্ভবত স্বর্ণমুদ্রার নাম ছিল দীনার ও রৌপ্যমুদ্রার নাম ছিল রূপক। ১৬ রূপক এক দীনারের সমান ছিল।
গুপ্তযুগের অবসানের পরে বাংলার স্বাধীন রাজগণ গুপ্তমুদ্রার অনুকরণে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত করেন কিন্তু তাঁহাদের কোনো রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যায় নাই। এই সমুদয় স্বর্ণমুদ্রার গঠন অনেক নিকৃষ্ট এবং ইহাতে খাদের পরিমাণও অনেক বেশি।
পালরাজগণ প্রায় চারিশত বৎসর এদেশে রাজত্ব করেন, কিন্তু তাঁহাদের মুদ্রা বড় বেশী পাওয়া যায় নাই। পাহাড়পুরে তিনটি তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, ইহার একদিকে একটি বৃষ ও অপরদিকে তিনটি মাছ উৎকীর্ণ। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এগুলি পালসাম্রাজ্যের প্রথম যুগের মুদ্রা। ‘শ্রী বিগ্র’ এই নামযুক্ত কতকগুলি তামা ও রূপার মুদ্রা পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন যে, এগুলি বিগ্রহপালের মুদ্রা। পালযুগের লিপিতে দ্রম্ম নামক মুদ্রার উল্লেখ আছে, সেইজন্য ঐ মুদ্রাগুলি বিগ্রহদ্রম্ম নামে অভিহিত হয়। এই স্বল্পসংখ্যক মুদ্রা ব্যতীত পালযুগের আর কোনো মুদ্রা আবিষ্কৃত না হওয়ায় এই যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা আমাদের নিকট অনেকটা জটিল হইয়া উঠিয়াছে। সেনযুগের লিপিতে পুরাণ ও কপর্দকপুরাণ নামে মুদ্রার উল্লেখ আছে। সম্ভবত একই প্রকার মুদ্রা এই দুই নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু সেনরাজগণের কোনো মুদ্রা এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। মীনহাজুদ্দিন লক্ষ্মণসেনের দানশীলতার উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, তিনি কাহাকেও লক্ষ কৌড়ির কম দান করিতেন না। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, তখন মুদ্রার পরিবর্তে কৌড়ি অথবা কড়ির প্রচলন ছিল। কিন্তু তাহা হইলে কপর্দক পুরাণের অর্থ কী? কেহ কেহ বলেন যে, ইহা কড়ির আকারে নির্ম্মিত রৌপ্যমুদ্রা। কিন্তু এরূপ একটি মুদ্রাও এযাবৎ পাওয়া যায় নাই। এইজন্য কেহ কেহ মনে করেন যে, কপর্দকপুরাণ বাস্তবিক কোনো মুদ্রার নাম নহে, একটি কাল্পনিক সংজ্ঞা মাত্র, এবং ইহাতে নির্দিষ্টসংখ্যক কড়ি বুঝাইত। এই রৌপ্যমুদ্রার পরিমাণে দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ হইত, কিন্তু বাস্ত বিক পক্ষে তদনুযায়ী কড়ি গুণিয়া দ্রব্যাদি কেনা হইত।
ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নত বাংলা দেশে কড়ির ব্যবহার ছিল, ইহাতে আশ্চৰ্য্য বোধ করিবার কোনো কারণ নাই। ভারতবর্ষে কড়ি প্রচলনের কথা ফাহিয়ান উল্লেখ করিয়াছেন। বাংলার চর্যাপদেও ইহার উল্লেখ আছে। ১৭৫০ অব্দে কলিকাতা শহরে ও বাজারে কড়ির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কিন্তু তথাপি গুপ্তযুগের পরবর্ত্তী বাংলার প্রসিদ্ধ রাজবংশগুলির, বিশেষত পাল ও সেনরাজগণের আমলে মুদ্রার অভাবের প্রকৃত কারণ কী-এ প্রশ্নের কোনো সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে।
২০. শিল্পকলা
বিংশ পরিচ্ছেদ – শিল্পকলা
১. স্থাপত্যশিল্প
প্রাচীন বাংলার স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাস লেখা অতিশয় কঠিন, কারণ হিন্দু যুগের প্রাসাদ, স্তূপ, মন্দির, বিহার প্রভৃতির কোনো চিহ্ন এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। ফাহিয়ান ও হুয়েন সাংয়ের বিবরণ এবং প্রাচীন শিলালিপি ও তাম্রশাসনগুলি আলোচনা করিলে কোনো সন্দেহ থাকে না যে, হিন্দু যুগে বাংলায় বিচিত্র কারুকার্যখচিত বহু হৰ্ম ও মন্দির এবং স্তূপ ও বিহার প্রভৃতি ছিল। কিন্তু এ সমুদয়ই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন প্রশস্তিকারেরা উচ্ছ্বসিত ভাষায় যে সমুদয় বিশাল গগনস্পর্শী মন্দির ‘ভূ-ভূষণ’, ‘কুল-পৰ্বত-সদৃশ’ অথবা সূর্যের গতিরোধকারী’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আজ তাঁহার চিহ্নমাত্রও নাই। দ্বাদশ শতাব্দীতেও সন্ধ্যাকরনন্দী বরেন্দ্রভূমিতে যে সমুদয় ‘প্রাংশু-প্রাসাদ’, মহাবিহার এবং কাঞ্চন-খচিত হৰ্ম্ম ও মন্দির দেখিয়াছিলেন, তাহা সবই কালগর্ভে বিলীন হইয়াছে। বাংলার স্থপতি-শিল্পের কীৰ্ত্তি আছে কিন্তু নিদর্শন নাই।
এদেশে প্রস্তর সুলভ নহে, তাই অধিকাংশ নির্মাণকার্য্যেই ইটের ব্যবহার হইত। আর্দ্র বায়ু, অতিরিক্ত বৃষ্টি, বর্ষা ও নদী প্লাবনের ফলে ইষ্টক শীঘ্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বৈদেশিক আক্রমণকারীর অত্যাচারেও অনেক বিনষ্ট হইয়াছে। প্রকৃতি ও মানুষ উভয়ে মিলিয়া বাংলার প্রাচীন শিল্পসম্পদ ভূপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছে।
সামান্য কয়েকটি ভগ্নপ্রায় মন্দির এই বিশ্বগ্রাসী ধ্বংসের হস্ত হইতে কোনো রকমে আত্মরক্ষা করিয়া এখনো দাঁড়াইয়া আছে। জঙ্গল-পরিপূর্ণ মৃৎস্তূপ খনন করিয়া পুরাতত্ত্ব-অনুসন্ধিৎসুগণ কোনো কোনো অতীত কীৰ্ত্তির জীর্ণ ধ্বংসাবশেষ আবার লোকচক্ষুর গোছর করিয়াছেন। ইহারাই বাংলার অতীত শিল্প-সম্পদের শেষ নিদর্শন। ইহাদের উপর নির্ভর করিয়াই বাংলার স্থাপত্যশিল্পের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করিতে হইবে। কিন্তু এ ইতিহাস নহে, ইতিহাসের কঙ্কাল মাত্র। বাংলার প্রাচীন শিল্প-সমৃদ্ধি এবং তাঁহার অতুলনীয় কীর্তি ও গৌরবের ক্ষীণ প্রতিধ্বনিও ইহার মধ্য দিয়ে ফুটিয়া উঠিবে কি না সন্দেহ।
.
ক। স্তূপ
বৌদ্ধস্তূপই ভারতের সর্বপ্রাচীন স্থাপত্য নিদর্শন। ভগবান বুদ্ধের অস্থি বা ব্যবহৃত বস্তু রক্ষা করিবার জন্যই প্রথম স্তূপের পরিকল্পনা হয়। পরে বিশেষ বিশেষ ঘটনা চিরস্মরণীয় করিবার জন্য যে যে স্থানে তাহা ঘটিয়াছিল সেখানে স্তূপ নির্ম্মিত হইত। বৌদ্ধদের পূর্ব্বেও হয়তো এই প্রথা ছিল-এবং পরে জৈনরাও স্তূপ নির্মাণ করিত। কিন্তু বৌদ্ধগণের মধ্যেই স্তূপ বিশেষ বিখ্যাত ছিল। বৌদ্ধগণ স্তূপকে পবিত্র মন্দিরের ন্যায় জ্ঞান করিত এবং পরবর্ত্তীকালে তাহারা স্তূপকেও পূজা ও অর্চনা করিত। স্তূপ নির্মাণ ও উৎসর্গ করা অতিশয় পুণ্য কাৰ্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। এই সমুদয় কারণে যেখানেই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রসারলাভ করিয়াছে সেইখানেই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অসংখ্য স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। বাংলা দেশেও অনেক স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল।
স্তূপের তিনটি অংশ। সৰ্ব্বপ্রাচীন স্থূপে অনুচ্চ গোলাকৃতি অধোভাগের উপর গম্বুজাকৃতি মধ্যম অথবা প্রধান অংশ এমনভাবে নির্ম্মিত হইত যাহাতে অধোভাগের কতকটা স্থান মুক্ত থাকে এবং ইহার উপর দিয়া গম্বুজের চারিদিকে ঘুরিয়া আসা যায়। এই উন্মুক্ত অংশ ভক্তগণের প্রদক্ষিণপথস্বরূপ ব্যবহৃত হইত। গম্বুজের উপর প্রথমত চতুষ্কোণ হৰ্ম্মিকা ও তাঁহার উপর একটি গোলাকৃতি চাকা থাকিত।
কালক্রমে স্তূপের আকৃতি ক্রমশই দীর্ঘাকার হইতে থাকে। অধোভাগ অনেকটা পিপার আকার ধারণ করে এবং মধ্যভাগের অর্দ্ধবৃত্তাকার গম্বুজও ক্রমশ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হয়। উপরের গোলচাকার সংখ্যাও বাড়িয়া যায় এবং পর পর ছোট হইতে হইতে সর্ব্বশেষ চাকাটি প্রায় বিন্দুতে পরিণত হয়। স্তূপের এই তিন অংশের নাম মেধি, অণ্ড ও ছত্রাবলী। ক্রমে এই তিন অংশের নীচে একটি অপোভাগ সংযুক্ত হয়। এই অধোভাগ চতুষ্কোণ, এবং ইহার প্রতি দিকের মধ্যভাগে খানিকটা অংশ সম্মুখে প্রসারিত থাকে। কোনো কোনো স্থলে এই প্রসারিত অংশের খানিকটাও আবার সম্মুখে প্রসারিত হয়। এইরূপ এক বা একাধিক প্রসারের ফলে অধোভাগ ক্রমশ ক্রসের আকার ধারণ করে। ক্রমশ নিচের এই ক্ৰসাকৃতি অধোভাগ ও মেধি এবং উপরের অসংখ্য ছত্রাবলীই প্রাধান্য লাভ করে, এবং এ দুয়ের মধ্যকার অংশ অণ্ড-এককালে যাহা স্তূপের প্রধান অংশ বলিয়া বিবেচিত হইত-আর দর্শকের মনোযোগ আকর্ষণ করে না। স্তূপগুলিও প্রায় মন্দির চূড়া বা শিখরের আকার ধারণ করে।
হুয়েন সাং লিখিয়াছেন যে পুণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট ও কর্ণসুবর্ণের যে যে স্থানে গৌতমবুদ্ধ ধর্মোপদেশ করিয়াছিলেন সেই সেই স্থানে মৌৰ্য্যসম্রাট অশোক নির্ম্মিত স্তূপগুলিও তিনি দেখিয়াছিলেন। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে হুয়েন সাংয়ের সময়ও বাংলার এমন বহু প্রাচীন স্তূপ ছিল যাহা লোকে অশোকের তৈরি বলিয়া বিশ্বাস করিত। কিন্তু বাস্তবিকই গৌতমবুদ্ধ যে ঐ সমুদয় স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন, এবং ইহার স্মরণার্থ অশোক ঐ সকল স্তূপ নিৰ্মাণ করিয়াছিলেন, অন্য প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত কেবল হুয়েন সাংয়ের উক্তির উপর নির্ভর করিয়া ইহার কোনোটিই বিশ্বাস করা যায় না। অশোকের কথা দূরে থাকুক, হুয়েন সাংয়ের সময়কার কোনো স্তূপের ধ্বংসাবশেষও অদ্যাবধি বাংলায় আবিষ্কৃত হয় নাই।
বাংলায় যে সকল স্তূপ দেখা যায় তাহা সাধারণত ক্ষুদ্রাকৃতি। পুণ্য অর্জনের জন্য দরিদ্র ভক্তগণ এইগুলি নিৰ্মাণ করিত।
ঢাকা জিলার আসরফপুর গ্রামে রাজা দেবখগের তাম্রশাসনের সহিত যে ব্ৰঞ্জ বা অষ্টধাতুনির্ম্মিত একটি স্তূপ পাওয়া গিয়াছে তাহাই সম্ভবত বাংলার সর্বপ্রাচীন স্তূপের নিদর্শন (চিত্র নং ২৬)। ইহার চতুষ্কোণ অধোভাগ ও হৰ্ম্মিকা এবং গোলাকার মেধির চতুর্দিকে নানা দেব-দেবীর মূর্ত্তি উৎকীর্ণ। স্তূপটির মেধি ও অণ্ড একটি ঘণ্টার মতো দেখায়। পাহাড়পুর ও চট্টগ্রামের অন্তর্গত ঝেওয়ারিতে আরও দুইটি ধাতুনির্ম্মিত স্তূপ পাওয়া গিয়াছে।
১০১৫ অব্দে লিখিত একখানি বৌদ্ধ গ্রন্থের পুঁথিতে বরেন্দ্রের মৃগস্থাপন-স্তূপের একটি চিত্র আছে। চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণ সপ্তম শতাব্দীতেও এই স্তূপটি দেখিয়াছিলেন। এই চিত্র হইতে সেকালেরর স্তূপের আকৃতি বেশ বোঝা যায়। এই স্তূপের অধোভাগ ছয়টি স্তরে বিভক্ত এবং প্রতিস্তরটি একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের আকার। অণ্ড অংশ ঈষৎ দীর্ঘাকৃতি এবং ইহার চতুর্দিকে চারিটি কুলুঙ্গির অভ্যন্তরে চারিটি বুদ্ধমূর্ত্তি। চতুষ্কোণ হৰ্ম্মিকার উপর বহুসংখ্যক ছত্র।
বৌদ্ধ গ্রন্থের পুঁথিতে বাংলার আরও দুই-তিনটি স্থূপের ছবি আছে। ইহার একটি তুলাক্ষেত্রে ‘বর্দ্ধমান স্তূপ’। ইহার অধোভাগ নানা কারুকার্যে শোভিত ও চারিটি স্তরে বিভক্ত, এবং ইহার মেধি উৰ্দ্ধ ও অধোমুখ দুই দল বিকশিত পদ্মের আকৃতি।
পাহাড়পুর ও বহুলাড়ায় (বাঁকুড়া) বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকস্থূপের অধোভাগ আবিষ্কৃত হইয়াছে (চিত্র নং ৩১)। এগুলি গোল, চতুষ্কোণ অথবা ক্রসের আকার। বিহারের প্রাচীন স্তূপ ও পূর্ব্বোক্ত বাংলার স্তূপের চিত্রের অধোভাগের সহিত ইহাদের অনেকের নিকট সাদৃশ্য দেখা যায়। সুতরাং এই সমুদয় অধোভাগের উপর যে সমুদয় স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহা দেখিতে বিহারের স্তূপ এবং মৃগস্থাপন অথবা বর্দ্ধমান স্তূপের ন্যায় ছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।
জোগী-গুফা নামক স্থানে পাথরের একটি ছোট স্তূপ পাওয়া গিয়াছে। ইহার মেধি ও অণ্ড অংশের উচ্চতা তাহাদের ব্যাসের তিন গুণ। সুতরাং মেধি অণ্ড ও ছত্রাবলী মিলিয়া ইহা একটি সুদীর্ঘ চূড়ার ন্যায় দেখায়, ইহাকে স্তূপ বলিয়া প্রথমে কিছুতেই মনে হয় না। ইহাকে বাংলার স্তূপের শেষ বিবর্ত্তন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।
.
খ। বিহার
সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বেই যে বাংলায় বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের বাসের জন্য অনেক বিহার ছিল এবং ইহার কোনো কোনোটি বেশ বড় ও কারুকার্যখচিত ছিল, চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণের বিবরণ হইতে তাহা জানা যায়। স্তূপের ন্যায় এগুলিও ধ্বংস হইয়াছে। কিন্তু রাজসাহীর অন্তর্গত পাহাড়পুর নামক স্থানে একটি বিশাল বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রাচীন বাংলার এই শ্রেণীর স্থাপত্যের সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা সম্ভবপর হইয়াছে।
একখানি তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, পঞ্চম শতাব্দীতেও এখানে একটি জৈন বিহার ছিল। সম্ভবত কালক্রমে ইহা নষ্ট হইয়া যায়। অষ্টম শতাব্দীতে ধর্ম্মপাল এখানে যে প্রকাণ্ড বিহার নির্মাণ করেন, সোমপুর মহাবিহার নামে তাহা ভারতের সর্বত্র এবং ভারতের বাহিরেও বৌদ্ধজগতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই প্রকাণ্ড বিহারের চতুষ্কোণ অঙ্গনটি প্রতিদিকে ২০০ গজ দীর্ঘ ছিল। (চিত্র নং ৩০)। অঙ্গনটি উচ্চ প্রাচীরে ঘেরা ছিল এবং অঙ্গনের চারিদিকেই এই প্রাচীরগাত্রে ভিক্ষুগণের বাসের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সমুদয় কক্ষের সংখ্যা ১৭৭। প্রতি কক্ষ প্রায় সাড়ে তেরো ফুট দীর্ঘ ছিল। কক্ষগুলির সম্মুখ দিয়ে আট-নয় ফুট চওড়া প্রশস্ত বারান্দা সমস্ত অঙ্গনটি ঘিরিয়া বিস্তৃত ছিল; এবং চারিদিকে চারিটি সিঁড়ি দিয়া বারান্দা হইতে অঙ্গনে নামা যাইত। প্রাচীরের উত্তর দিকে এই বিহারের প্রধান প্রবেশপথ অথবা সিংহদরজা ছিল। ইহার পশ্চাতেই একটি প্রকাণ্ড স্তম্ভযুক্ত প্রশস্ত দালান ছিল। এই দালান হইতে আর একটি ক্ষুদ্রতম স্তম্ভযুক্ত দালানের মধ্য দিয়া পূর্ব্বোক্ত কক্ষ শ্রেণীর সম্মুখস্থ বারান্দায় পৌঁছানো যাইত। দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম বারান্দায় ঠিক মধ্যস্থলে, অঙ্গনে নামিবার সিঁড়ির পশ্চাতেও এইরূপ কয়েকটি অতিরিক্ত কক্ষ ছিল। সমুদয় কক্ষগুলি হইতে জল নিঃসারণের জন্য পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থা ছিল। বিস্তৃত অঙ্গনের ঠিক মধ্যস্থলে একটি প্রকাণ্ড মন্দির ছিল (চিত্র নং ৩১)। এই মন্দির ও চতুস্পার্শ্বস্থ কক্ষগুলির মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত আঙ্গিনায় ছোট ছোট স্তূপ, মন্দির, কূপ, স্নানাগার, রন্ধনশালা ভোজনালয় প্রভৃতি ছিল। ভারতবর্ষে এ পর্য্যন্ত যত বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাঁহার মধ্যে এই সোমপুর বিহারই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই বিহারটি যখন সম্পূর্ণ ছিল তখন ইহার বিশালত্ব ও সৌন্দর্য্য লোকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিত। একখানি সমসাময়িক লিপিতে ইহা “জগতাং নেকৈবিশ্রাম-ভূ” (জগতে নয়নের একমাত্র বিরামস্থল অর্থাৎ দর্শনীয় বস্তু) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহার মহাবিহার নাম সার্থক ছিল।
সম্প্রতি কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী ময়নামতী নামক অনুচ্চ পর্বতমালায় কয়েকটি বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহার খননকার্য এখনো আরম্ভ হয় নাই, কিন্তু প্রাথমিক পরীক্ষার ফলে একজন পুরাতত্ত্ববিৎ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পাহাড়পুরের বিহার ও মন্দির অপেক্ষাও বৃহত্তর বিহার ও মন্দিরাদি এইখানে ছিল।
এই সমুদয় ধ্বংসাবশেষ হইতেই প্রাচীন বাংলার বিহার সম্বন্ধে কতক ধারণা করা যায়।
.
গ। মন্দির
বাংলার প্রাচীনকালের মন্দির প্রায় সকলই ধ্বংস হইয়াছে এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কিন্তু কোনো কোনো বৌদ্ধ গ্রন্থের পুঁথিতে কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরের ছবি আছে। কতকগুলি প্রস্তরমূর্ত্তিতেও মন্দির উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই সমুদয় প্রতিকৃতির সাহায্যে বাংলার প্রাচীন মন্দিরের গঠনপ্রণালী আলোচনা করিলে ছাদের আকৃতি অনুসারে ইহা নিম্নলিখিত চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।
১। এই শ্রেণীর মন্দিরের ছাদ উপর্যুপরি কতকগুলি সামন্তরাল চতুষ্কোণ স্ত রের সমষ্টি। প্রতি দুই স্তরের মধ্যবর্ত্তী ভাগ অন্তর্নিবিষ্ট থাকায় এই স্তরগুলি বেশ পৃথক পৃথক দেখা যায়। স্তরগুলি যত ঊর্ধ্বে উঠিতে থাকে ততই ছোট হয়। গুপ্তযুগের ভাস্কর্যে এই শ্রেণীর মন্দির উত্তীর্ণ হইয়াছে। ইহার পরিণতি দেখা যায় উড়িষ্যার মন্দিরের সম্মুখস্থ জগমোহনে। উড়িষ্যার এই প্রকার ছাদযুক্ত মন্দির ভদ্র অথবা নীড় দেউল নামে অভিহিত হইয়াছে।
২। দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্দিরের ছাদ উড়িষ্যার মন্দিরের ন্যায় শিখরে ঢাকা। চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের প্রাচীরগাত্র হইতে উচ্চ শিখরের চারিটি ধার উঠিয়া ঈষৎ বাঁকা হইতে হইতে অবশেষে প্রায় সংলগ্ন হইয়া যায়। এই সংযোগস্থল একটি গোলাকার প্রস্তরখণ্ডে (আমলক শিলা) আবদ্ধ করা হয় এবং শিখরের গাত্রে কারুকার্যখচিত অনেক লম্বালম্বি পংক্তি থাকে। এই শ্রেণীর মন্দিরের নাম রেখ-দেউল।
৩-৪। প্রথম শ্রেণীর ভদ্র দেউলের সর্বোচ্চ স্তরের উপর একটি স্তূপ বা শিখর স্থাপিত করিয়া এই দুই শ্রেণীর মন্দিরের সৃষ্টি হইয়াছে। কোনো কোনো স্থলে এই স্তূপ বা শিখর কেবল সর্বোচ্চ স্তরের উপরে নহে, প্রতি স্তরের কোণে এবং সম্মুখ ভাগেও দেখা যায়।
বৌদ্ধ পুঁথির চিত্র ও প্রস্তরমূৰ্ত্তি হইতে জানা যায় যে, প্রাচীন বাংলায় এই চারি শ্রেণীর মন্দির ছিল। তবে শেষোক্ত দুই শ্রেণীর কোনো প্রাচীন মন্দির এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে নির্ম্মিত দিনাজপুরের অন্তর্গত কান্তনগরের মন্দির চতুর্থ শ্রেণীর মন্দিরের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া গণ্য করা যাইতে যারে। ব্রহ্মদেশে এইরূপ মন্দির আছে। বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর মন্দিরের অঙ্গনে নন্দীর যে ক্ষুদ্র একটি মন্দির আছে, প্রথম শ্রেণীর মন্দিরের তাহাই একমাত্র নিদর্শন। এতদ্ব্যতীত বাংলায় যে কয়েকটি প্রাচীন মন্দির আছে তাহা সকলই দ্বিতীয় শ্রেণীর। ইহার মধ্যে বর্দ্ধমানের অন্তর্গত বরাকরে একটি, ও বাঁকুড়ার অন্তর্গত দেহারে দুইটি, মোট তিনটি প্রস্তরে গঠিত, অবশিষ্ট ককেটি ইষ্টকনিৰ্মিত। এই মন্দিরগুলির শিখর পূর্ব্বোক্ত বর্ণনানুযায়ী ও উড়িষ্যার মন্দিরের অনুরূপ। হিন্দু যুগে এই শ্রেণীর মন্দির উত্তর ভারতের সর্বত্র দেখা যাইত।
বরাকরের ৪ নং মন্দিরটি (চিত্র নং ৩) ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রাচীন। ইহার অপেক্ষাকৃত উচ্চ গর্ভগৃহ, অনুচ্চ শিখরভাগ এবং আমলক শিলার আকৃতি অনেকটা ভুবনেশ্বরের প্রাচীন পরশুরামেশ্বর মন্দিরের ন্যায়, এবং ইহা সম্ভবত ঐ সময় অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দে নির্ম্মিত।
বড় বড় মন্দিরের অনুকরণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দিরও নির্ম্মিত হইত। রাজসাহী জিলার অন্তর্গত নিমদীঘি এবং দিনাজপুরের অন্তর্গত বাণগড়ে এইরূপ প্রস্তরনির্ম্মিত দুইটি এবং চট্টগ্রামের অন্তর্গত ঝেওয়ারিতে ব্ৰঞ্জনির্ম্মিত একটি মন্দির (চিত্র নং ৪) পাওয়া গিয়াছে। এগুলির গঠনপ্রণালী একই রকমের এবং সম্ভবত বরাকর মন্দিরের অনতিকাল পরেই এই সমুদয় নির্ম্মিত হয়। এই যুগের বৃহৎ শিখরযুক্ত মন্দির কিরূপ কারুকার্যখচিত ছিল এই সমুদয় দেখিলে তাহা অনেকটা অনুমান করা যায়। গর্ভগৃহের চতুর্দিকে চারিটি ত্রিভঙ্গিম খিলানযুক্ত কুলুঙ্গি, শিখরগাত্রে অলঙ্কাররূপে চৈত্যগবাক্ষের ব্যবহার, এবং শিখরের উপরিভাগে চারি কোণে সিংহমূৰ্ত্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
পরবর্ত্তীকালের মন্দিরগুলিতে খোদিত কারুকাৰ্য্য অনেক বেশি। শিখরের কোণগুলি পালিশ করায় ইহা অধিকতর গোলাকার দেখা যায় এবং শিখরগাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখরের প্রতিমূর্ত্তি উত্তীর্ণ করা হয়। মন্দিরের প্রবেশপথের সম্মুখস্থ পুরু দেওয়ালের মধ্যে একটু ছোট নাটমন্দিরের মতো কক্ষ যোগ করাও এগুলির আর একটি বিশেষত্ব। দেউলিয়ার (বর্দ্ধমান) মন্দির, বহুলারার (বাঁকুড়া) সিদ্ধেশ্বর মন্দির (চিত্র নং ২৭ ক), (সুন্দরবনের জটার দেউল) এবং দেহারের (বাঁকুড়া) সরেশ্বর ও সল্লেশ্বরের মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম তিনটি ইষ্টক ও শেষোক্ত দুইটি প্রস্তরে নির্ম্মিত। সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের কারুকার্য বাংলার মন্দিরশিল্পের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।
পাহাড়পুরের বিহারের অঙ্গনের ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটি বিশাল মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে (চিত্র নং ৩১)। ইহার ঊর্ধ্বভাগ বিলুপ্ত হওয়ায় এই মন্দিরটি কোন শ্রেণীর অন্তর্গত ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু ইহার নিচের যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাহা ভারতবর্ষের অন্যান্য মন্দির হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।
মন্দিরটি ত্রিতল। ইহার ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটি চতুষ্কোণ বর্গাকৃতি অংশ সোজা উপরে উঠিয়া গিয়াছে। ইহার চারিধারের প্রাচীর অতিশয় স্কুল ও দৃঢ় এবং প্রাচীরের অভ্যন্তরস্থ স্থান ফাঁকা হইলেও সেখানে প্রবেশ করিবার কোনো উপায় নাই। ত্রিতলে এই বর্গাকৃতি অংশের প্রতি প্রাচীরের সম্মুখভাগে একটী নাটমন্দির ও মণ্ডপ এমনভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে যাহাতে ইহার দুই পার্শ্বে প্রাচীরের খানিক অংশ মুক্ত থাকে। ইহার ফলে এই চারিটি প্রসারিত অংশের মধ্যে বর্গাকৃতি অংশের চারিটি কোণ বাহির হইয়া আছে এবং সমস্তটা একটি ক্রসের আকার ধারণ করিয়াছে। এই ক্রসের সীমারেখা অনুযায়ী একটি প্রদক্ষিণপথ ও তাঁহার আবেষ্টনী মন্দিরের চারিদিকে ঘিরিয়া আছে। দ্বিতলের পরিকল্পনা ত্রিতলেরই অনুরূপ-কিন্তু ইহার প্রতিদিকের সম্মুখভাগ খানিকটা প্রসারিত করিয়া আরও দুইটি কোণের সৃষ্টি করা হইয়াছে। একতল দ্বিতলের অনুরূপ, কেবল ইহার উত্তর দিকের একটু অংশ বাড়াইয়া সিঁড়ির জায়গা করা হইয়াছে। সমগ্র মন্দিরটি উত্তর-দক্ষিণে ৩৫৬ ফুট এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৩২৪ ফুট দীর্ঘ। যে অংশ অবশিষ্ট আছে তাঁহার উচ্চতা ৭০ ফুট।
এই বিশাল মন্দিরের উপরিভাগ কিরূপ ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে বর্গাকৃতি অংশের উপরে মূল মন্দির ছিল। আবার কেহ কেহ বলেন যে সাধারণ মন্দিরের গর্ভগৃহের ন্যায় কোনো কক্ষ এই মন্দিরে ছিল না-কেবল বর্গাকৃতি অংশের সম্মুখস্থ চারিটি নাটমন্দিরে চারিটি দেবমূর্ত্তি ছিল। জৈন চতুর্মুখ মন্দির ও ব্রহ্মদেশের কোনো কোনো মন্দিরে এইরূপ ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়।
সম্ভবত বর্গাকৃতি অংশের উপর এক উচ্চ শিখর ছিল, এবং যাহাতে এই বিশাল শিখরের ভার বহন করিতে পারে সেই জন্যই বর্গাকৃতি অংশ এমন সুদৃঢ়ভাবে একেবারে নীচ হইতে গাঁথিয়া ভোলা হইয়াছিল। যখন এই বিশাল মন্দিরের উপযোগী উচ্চ শিখর বিদ্যমান ছিল তখন ইহা বহুদূর হইতে গিরিচূড়ার ন্যায় দেখা যাইত, এবং ইহার সৌন্দৰ্য্য, বিশালতা ও গাম্ভীর্য লোকের মনে কিরূপ বিস্ময় উৎপাদন করিত, আজ আমরা কেবলমাত্র কল্পনায় তাহা অনুভব করিতে পারি।
মন্দিরটি ইট-কাদার গাঁথুনিতে তৈরী, অথচ সহস্রাধিক বৎসর পরে আজিও এই ইটের দেওয়াল ৭০ ফুট উঁচু পর্য্যন্ত অবশিষ্ট আছে ইহাই আশ্চর্যের বিষয়। দেওয়ালের মাঝে মাঝে কারুকার্যখোদিত ইটের কার্নিশ এবং দেওয়ালের গায়ে আবদ্ধ তিনটি সারিতে সাজানো পোড়ামাটি ও প্রস্তর ভাস্কর্যের ফলকগুলি এখনো ইহার অতীত শিল্পকলার নিদর্শনরূপে বর্ত্তমান। মন্দিরটি অষ্টম শতাব্দে নির্ম্মিত কিন্তু ইহার গাত্রসংলগ্ন কোনো কোনো ভাস্কৰ্য্য গুপ্তযুগের। সম্ভবত কোনো প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হইতে এগুলি আহৃত হইয়া পরবর্ত্তীকালের মন্দিরগাত্রে সংলগ্ন করা হইয়াছে।
পাহাড়পুরের মন্দিরের পরিকল্পনা ভারতবর্ষে আর কোনো স্থানে দেখা যায় না, কিন্তু যবদ্বীপ ও ব্রহ্মদেশের কোনো কোনো মন্দির অনেকটা এইরূপ এবং ইহারই অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। পূৰ্বোক্ত বাংলার তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর মন্দিরের শিখরও ব্রহ্মদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বঙ্গদেশের অধুনা বিলুপ্ত মন্দিরশিল্প সুদূর প্রাচ্যের হিন্দু উপনিবেশগুলিতে বিশেষ প্রভাব বিস্ত রি করিয়াছিল এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। বাংলায় প্রাচীন মন্দির খুব বেশি নাই, কিন্তু এই সমুদয় মন্দিরের অংশবিশেষ-স্তম্ভ, চৌকাঠ প্রভৃতি-নানা স্থানে পাওয়া গিয়াছে। দিনাজপুর রাজবাড়ীতে কারুকার্যখচিত একটি প্রস্তরস্তম্ভ আছে। ইহার গাত্রের উত্তীর্ণ লিপি হইতে জানা যায় যে স্তম্ভটি গৌড়াধিপ প্রতিষ্ঠিত একটি শিবমন্দিরের অংশ। এই মন্দিরটি নবম শতাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বীরভূম জিলার অন্তর্গত পাইকোরে দুইটি এবং পাবনা জিলার হাণ্ডিয়াল গ্রামে চারিটি বিচিত্র কারুকার্যে শোভিত প্রস্তরস্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে। দিনাজপুরের গরুড় স্তম্ভ ও কৈবৰ্ত্ত স্তম্ভও (চিত্র নং ২৮ ক) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিক্রমপুরের নানা স্থানে প্রস্তর ও কাষ্ঠের স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে। কাষ্ঠের স্তম্ভগুলি জীর্ণ হইলেও তাঁহার গাত্রে উত্তীর্ণ বিচিত্র কারুকার্য এখনো দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ইহার শিল্পকলা অতিশয় উচ্চশ্রেণীর। এইরূপ কয়েকটি কাষ্ঠের স্তম্ভ, ব্রাকেট প্রভৃতি ঢাকা যাদুঘরে। রক্ষিত আছে, এবং এইগুলি প্রাচীন বাংলার দারুশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন (চিত্র নং ২৯)। ইহা হইতে আরও প্রমাণিত হয় যে বাংলায় কাষ্ঠনির্ম্মিত অনেক মন্দির ছিল। কালক্রমে সেগুলি ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার যে দুই-একটি ক্ষুদ্র অংশ প্রায় সহস্র বৎসর পরেও টিকিয়া আছে তাহা হইতেই এই মন্দিরগুলির সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কতকটা ধারণা করা যাইতে পারে। স্তম্ভগুলি বাস্তবিক বাংলার বিলুপ্ত মন্দিরশিল্পের স্মৃতিস্তম্ভ।
বাণগড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আবিষ্কৃত একটি বিশাল কারুকার্যখচিত পাথরের চৌকাঠ এখন দিনাজপুর রাজবাড়ীতে আছে। প্রাচীন গৌড়ে ও রাজসাহী জিলায় কয়েকটি পাথরের চৌকাঠের অংশ পাওয়া গিয়াছে। এগুলির কারুকার্য খুবই উচ্চদরের। স্তম্ভের ন্যায় এই সমুদয় চৌকাঠও প্রাচীন মন্দিরশিল্পের স্মৃতি বহন করিতেছে।
.
২. ভাস্কৰ্য্য
ভারতবর্ষে চিরকাল দেবমন্দিরই স্থাপত্য ও ভাস্কৰ্য্যশিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল। প্রাচীন বাংলায় মন্দির ছিল, সুতরাং ভাস্কর্যের বহু উন্নতি হইয়াছিল। মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে ইহার অধিকাংশই লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু অনেক স্থলে মন্দির বিনষ্ট হইলেও তন্মধ্যস্থ দেবমূৰ্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে। বাংলায় যে বহুসংখ্যক দেব-দেবীর মূৰ্ত্তি পাওয়া গিয়াছে পূর্ব্বেই তাঁহার উল্লেখ করিয়াছি। এই সমুদয় মূর্ত্তি হইতে বাংলার প্রাচীন চারুশিল্পের কতক পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার অধিকাংশই নবম শতাব্দীর পরবর্ত্তীকালের। ইহার পূর্ব্বে একমাত্র পাহাড়পুর মন্দিরগাত্রেই অনেক ভাস্কর্যের নিদর্শন একত্র পাওয়া যায়। যে সমস্ত ভাস্কর্যের নিদর্শন ইহারও পূৰ্ব্ববর্ত্তীকালে বলিয়া নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যায় তাঁহার সংখ্যা খুবই অল্প।
ক। প্রাচীন যুগ
চন্দ্রবর্ম্মার রাজধানী পুষ্করণা (বাঁকুড়া জিলার পোকৰ্ণা) ও সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন নগরী তাম্রলিপ্তিতে প্রাপ্ত কয়েকখানি উত্তীর্ণ পোড়ামাটি বাংলার সৰ্ব্বপ্রাচীন ভাস্কর্যের নিদর্শন। ইহার একখানিতে একটি যক্ষিনীর মূর্ত্তি আছে। ইহার গঠনপ্রণালী ও বসন-ভূষণ শুঙ্গযুগের মূর্ত্তির অনুরূপ (খৃ. পৃ. প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দী)। মহাস্থানে একটি পোড়ামাটির মূৰ্ত্তি কেহ কেহ মৌর্য যুগের বলিয়া মনে করেন, কিন্তু ইহা এতই অস্পষ্ট যে এ সম্বন্ধে কোনো সঠিক ধারণা করা কঠিন। মহাস্থানের আর একটি পোড়ামাটির মূর্ত্তি সম্ভবত শুঙ্গযুগের।
রাজসাহী জিলার অন্তর্গত কুমারপুর ও নিয়ামপুরে প্রাপ্ত দুইটি সূৰ্য্যমূর্ত্তি এবং মালদহ জিলার হাঁকরাইল গ্রামের বিষ্ণুমূর্ত্তির পোশাক-পরিচ্ছদ ও গঠনপ্রণালী কুষাণযুগের মূর্ত্তির অনুরূপ। বাণগড়ে প্রাপ্ত কয়েকটি পোড়ামাটির মূর্ত্তিতে কুষাণ অথবা তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগের শিল্প-লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়।
বিহারৈলের বুদ্ধমুর্তি সারনাথের গুপ্তযুগের মূর্ত্তির অবিকল অনুকরণ বলিলেও চলে। কাশীপুরের (সুন্দরবন) ও দেওরার (বগুড়া) সূৰ্য্যমূৰ্ত্তি দুইটিতেও গুপ্তযুগের শেষকালের (ষষ্ঠ শতাব্দী) শিল্প-লক্ষণ বিদ্যমান। ইহাদের মধ্যে কাশীপুরের মূর্ত্তিটি (চিত্র নং ১৫ক) অধিকতর সৌষ্ঠবসম্পন্ন। গুপ্তযুগে পূৰ্ব্ব ভারতীয় মূর্ত্তিগুলিতে যেরূপ সংযম ও গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে কমনীয়তা ও ভাবপ্রবণতার অপূৰ্ব্ব সমাবেশ দেখা যায়, এই মূর্ত্তিটিতে তাহা বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। মহাস্থানের নিকটবর্ত্তী বলাইধাপ ভিটায় সোনার পাতে ঢাকা অষ্টধাতুনির্ম্মিত একটি মঞ্জুশ্রী মূৰ্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই মূর্ত্তিটি প্রাচীন বাংলার ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। ইহার গঠনপ্রণালী গুপ্তযুগের আদর্শের অনুযায়ী। এই মূর্ত্তির কমনীয় অথচ শান্ত-সমাহিতভাবে পরিপূর্ণ মুখশ্রী, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের লাবণ্য ও সুষমা, করাঙ্গুলি, অধর-যুগলের ব্যঞ্জনা ও সমগ্র দেহের ভাবপ্রবণতা দেখিলে, প্রাচীন বাংলায় চারুশিল্পের কত দূর উৎকর্ষ হইয়াছিল, তাঁহার ধারণা করা যায়।
এই সমুদয় মূৰ্ত্তি হইতে প্রমাণিত হয় যে, খৃষ্টাব্দের আরম্ভ বা তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই বাংলায় ভাস্কর্যের চর্চ্চা ছিল এবং বাংলার শিল্পী গুপ্তযুগ পৰ্য্যন্ত ভারতের সাধারণ শিল্পধারার সহিত যোগ রক্ষা করিয়াই চলিত। ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে বাংলার ভাস্কর্যে কোনো বিশিষ্ট প্রণালী বা পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায় না। এই পরিচয় প্রথম পাওয়া যায় দেবখড়ের রাণী প্রভাবতীর লিপিযুক্ত সৰ্ব্বাণী ও তাঁহার সহিত প্রাপ্ত একটি ক্ষুদ্র সূৰ্য্যমূৰ্ত্তিতে। এই দুইটি সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে নির্ম্মিত। গুপ্তশিল্পের প্রভাব থাকিলেও, ইহাতে পরবর্ত্তী পালযুগের শিল্প-বৈশিষ্ট্যের সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত মণিরহাটে প্রাপ্ত একটি শিবমূৰ্ত্তিও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই তিনটি মূর্ত্তিই ধাতুনির্ম্মিত।
.
খ। পাহাড়পুর
পাহাড়পুরের মন্দিরগাত্রে যে খোদিত প্রস্তর ও পোড়ামাটির ফলক আছে তাহা হইতে সর্বপ্রথমে বাংলার নিজস্ব ভাস্কৰ্য্যশিল্পের বৈশিষ্ট্যের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। বিষয়বস্তু ও শিল্পকৌশলের দিক দিয়া বিচার করিলে, পাহাড়পুরের ভাস্কৰ্য্য দুই বা তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমটি লোকশিল্প এবং দ্বিতীয়টি অভিজাত শিল্প। তৃতীয়টি এ দুয়ের মাঝামাঝি।
প্রস্তরের কয়েকটি ও পোড়া-মাটির সমুদয় ফলকগুলি প্রথম শ্রেণী অথবা লোকশিল্পের অন্তর্ভুক্ত। রামায়ণ-মহাভারতের অনেক কাহিনী ইহাতে খোদিত হইয়াছে। কৃষ্ণের জন্মকথা এবং যে সমুদয় লীলা বাঙ্গালীর চিরপ্রিয় এবং বাংলার প্রতি ঘরে পরিচিত, তাঁহার বহু দৃশ্য ইহাতে আছে (চিত্র নং ৭-৮)। পঞ্চতন্ত্র ও বৃহকথার জনপ্রিয় গল্প ইহার হাস্যরসের আধার যোগাইয়াছে। সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ ও জীবনযাত্রার দৈনন্দিন কাহিনী ইহাতে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মেয়েরা নানা ভঙ্গীতে নৃত্য করিতেছে (চিত্র নং ৬), শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া জননী কূপ হইতে জল তুলিতেছে অথবা জলের কলসীসহ গৃহে ফিরিতেছে, কৃষক লাঙ্গল কাঁধে করিয়া মাঠে যাইতেছে, বাজিকর কঠিন কঠিন বাজি দেখাইতেছে, শীর্ণকায় সাধু-সন্ন্যাসী কাঁধের উপর কাষ্ঠখণ্ডের সাহায্যে তৈজসপত্র বহন করিয়া লম্বা দাড়ি ঝুলাইয়া নজদেহে চলিয়াছে, পরচুলাপরা দারোয়ান লাঠি ভর দিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঝিমাইতেছে। (চিত্র নং ৫), প্রেমালাপে মত্ত যুবক-যুবতী, পুরুষ ও স্ত্রী বাদ্যকারগণ এবং তাহাদের বাদ্যযন্ত্র, পূজানিরত ব্রাহ্মণ, অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পুরুষ ও নারী, ধনুর্বাণহস্তে রথারোহী যোদ্ধা, পর্ণমাত্ৰ-পরিহিত শবর স্ত্রী-পুরুষের প্রেমালাপ, ধনুহস্তে শবর, মৃত জন্তু হস্তে লইয়া বীরদর্পে পদক্ষেপকারিণী শবর রমণী,-এইরূপ অসংখ্য দৃশ্য শিল্পী খোদাই করিয়াছে। সুপরিচিত পশুপক্ষী পত্রপুষ্প গাছপালাও শিল্পীর দৃষ্টি এড়ায় নাই। দৃশ্যমান জগতের বাহিরেও শিল্পীর কল্পনা বিস্তার লাভ করিয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, গণেশ, বোধিসত্ত্ব, পদ্মপাণি, মঞ্জুশ্রী, তারা প্রভৃতি দেব-দেবীর মূর্ত্তি আছে, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা খুব বেশি নহে। দৈত্য, দানব, নাগ, কিন্নর, গন্ধৰ্ব্ব ও বহু কাল্পনিক জীবজন্তু শিল্পীর হস্তে মূর্ত্তি পরিগ্রহণ করিয়াছে।
যে সকল ভাস্কর এই সমুদয় দৃশ্য খোদিত করিয়াছিল, তাহাদের শিক্ষা ও সমাজ খুব উচ্চশ্রেণীর নহে। উত্তীর্ণ পুরুষ ও নারীমূর্ত্তির গঠন অতি সাধারণ, এমনকি কুৎসিত বলাও চলে। তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সৌষ্ঠবহীন এবং অনেক সময় অস্বাভাবিক, পরিধেয় বসন-ভূষণ অতিশয় সংক্ষিপ্ত ও সাধারণ; তাহাদের গতি ও ভঙ্গীর মধ্যে কোনো লাবণ্য বা সুষমা নাই এবং অন্তর্নিহিত কোনো ভাব বা চিন্তা তাহাদের মুখশ্রীতে ফুটিয়া ওঠে নাই। যে সূক্ষ্ম সৌন্দৰ্য্যানুভূতি উচ্চ শিল্পের প্রাণ, এই সমুদয় মূর্ত্তিতে তাঁহার সম্পূর্ণ অভাব। কিন্তু উচ্চাঙ্গের সৌন্দৰ্যবোধ বা প্রকাশের ক্ষমতা না থাকিলেও সংসার ও সমাজের সহিত এই সমুদয় ভাস্করের ঘনিষ্ঠ পরিচয়, নিকট সম্বন্ধ ও নিবিড় সহানুভূতি ছিল, এবং তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা অপরিণত হইলেও পুরুষানুক্রমলব্ধ কৌশল ও স্বাভাবিক নিপুণতার সাহায্যে তাহারা সরল অকৃত্রিমভাবে ইহার পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছে। সংখ্যায় অগণিত যে সমুদয় সাধারণ শ্রেণীর নর-নারী উচ্চতর শিল্প বা সৌন্দৰ্য্যবোধের দাবি করিত, তাহাদের জন্যই এই সমুদয় শিল্প রচনা। তাহারা যে এই দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিচিত দৃশ্যাবলী এবং কাল্পনিক ও বাস্তব জগতের চিত্র বিশেষভাবে উপভোগ করিত, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই হিসেবে পাহাড়পুরের এই দৃশ্যাবলী বাংলার প্রাচীন লোকশিল্পের চমৎকার দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।
কিন্তু বাংলায় যে উচ্চশ্রেণীর শিল্পীও ছিল পাহাড়পুরের দ্বিতীয় শ্রেণীর পাথরের ফলকে উত্তীর্ণ মূর্ত্তিগুলিই তাঁহার প্রমাণ। এগুলির সংখ্যা খুব বেশী নহে, এবং ইহারা প্রধানত কৃষ্ণ, বলরাম, শিব, যমুনা প্রভৃতি দেব-দেবীর মূর্ত্তি (চিত্র নং ৯)। ইহার মধ্যে একটি পুরুষ ও নারীর প্রণয়চিত্র (চিত্র নং ৮) অনেকেই রাধাকৃষ্ণের যুগলমূৰ্ত্তি বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মূর্ত্তির মস্তকের পশ্চাতে দিব্যজ্যোতির চিহ্ন আছে, অতএব ইহা সাধারণ মনুষ্যমূৰ্ত্তি নহে। কৃষ্ণের জীবনের অনেক দৃশ্য এই মন্দিরগাত্রে আছে। সুতরাং খুব সম্ভবত ইহা কৃষ্ণ ও তাঁহার প্রেয়সীর মূর্ত্তি। কিন্তু এই প্রেয়সী যে রাধা এরূপ মনে করিবার বিশেষ কোনো কারণ নাই। কৃষ্ণ-রাধার প্রেমের কাহিনী মহাভারত ও প্রাচীন পুরাণাদিতে পাওয়া যায় না এবং ইহা যে এই সময়ে প্রচলিত ছিল, তাঁহারও কোনো সন্তোষজনক প্রমাণ নাই। সুতরাং অনেকে মনে করেন যে, ইহা কৃষ্ণের পার্শ্বে রুক্মিণী অথবা সত্যভামার মূর্ত্তি।
এই মূর্ত্তির সহিত পূর্ব্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত অনুরূপ কয়েকটি প্রণয়িযুগলের মূৰ্ত্তি তুলনা করিলেই শিল্প হিসাবে এ দুয়ের প্রভেদ বুঝিতে পারা যাইবে। মুখশ্রী, দাঁড়াইবার ভঙ্গি, নারীমূৰ্ত্তির ঈষৎ বক্র লীলায়িত দৃষ্টিভঙ্গী ও সলাজ-হাস্য-ফুরিতাধর, হস্তপদাদির গঠন-সৌষ্ঠব, পরিধেয় বসনের রচনাপ্রণালী, এবং সর্বোপরি নর-নারীর প্রেমের যে একটি মাধুৰ্য্য ও মহিমা এই মূর্ত্তির মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, এই সমুদয় বিষয় বিবেচনা করিলে, ইহার শিল্পীর শিক্ষা দীক্ষা ও সৌন্দৰ্য্যানুভূতি যে পূর্ব্বোক্ত শিল্পীগণের অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরের সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। বলরাম ও যমুনার মূর্ত্তির সহিত যম, অগ্নি প্রভৃতির এবং দক্ষিণ প্রাচীরস্থিত শিবমূৰ্ত্তির সহিত অন্যান্য শিবমূর্ত্তির তুলনা করিলেও স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, পাহাড়পুরের প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গুপ্তযুগের গঠন-সৌষ্ঠব, অঙ্গের লাবণ্য ও সুষমা, গতিভঙ্গীর বৈচিত্র্য ও সাবলীল ভাব, অন্তর্নিহিত ভাবের বিকাশে উদ্ভাসিত মুখশ্রী প্রভৃতির স্পষ্ট নিদর্শন দেখা যায়। বাংলার যে সমুদয় শিল্পী এগুলি গড়িয়াছিল গুপ্তযুগের শিল্পই তাহাদের আদর্শ ছিল, এবং স্বাভাবিক প্রতিভা ও কঠোর সাধনা দ্বারা তাহারা তদনুযায়ী শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। প্রথম শ্রেণীর শিল্পীদের শিক্ষা ও আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে প্রাচীনকাল হইতে যে শিল্পধারা সহজ ও স্বাভাবিক বিবর্ত্তনের ফলে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহারা শিশুকাল হইতেই অভ্যস্ত হইয়া তাহাকে রূপ দিয়াছিল।
পাহাড়পুরে কতকগুলি খোদিত প্রস্তর আছে যাহাতে প্রথম শ্রেণীর অপটুতা ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষা ও সৌন্দর্যবোধ উভয়ই আংশিকভাবে বর্ত্তমান। কৃষ্ণের কয়েকটি বাল্যলীলা ও কতকগুলি দেব-দেবী ও দিকপালের মূৰ্ত্তি এই শ্রেণীর অন্ত গত। কৃষ্ণের কেশীবধ (চিত্র নং ৭) ইহার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। বালকৃষ্ণের মূর্ত্তি এবং ইহার সাবলীল গতিভঙ্গী দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পীর অনুযায়ী, কিন্তু ইহার মুখ চোখের গঠনে পারিপাট্যের যথেষ্ট অভাব। ইন্দ্রের মূর্ত্তির মধ্যেও যথেষ্ট সৌষ্ঠব ও সৌন্দৰ্য্য আছে, কিন্তু ইহার চোখ ও মুখের গঠন অত্যন্ত অস্বাভাবিক। এই সমুদয় কারণে এই খোদিত প্রস্তরগুলি একটি পৃথক বা তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। সম্ভবত বাংলার প্রাচীন শিল্প ও গুপ্তযুগের নূতন আদর্শ এই দুয়ের সংমিশ্রণে ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল।
প্রথম শ্রেণীর খোদিত পোড়া-মাটি ও পাথরগুলি যে পাহাড়পুর মন্দিরের সমসাময়িক, সে বিষয়ে সকলেই একমত; কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর খোদিত পাথরগুলি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। সম্ভবত এগুলি কোনো মন্দিরগাত্রে সংলগ্ন ছিল, পরে পাহাড়পুর মন্দিরে ব্যবহার করা হইয়াছে। কিন্তু এই বিভিন্ন শ্রেণীর শিল্প যে বিভিন্ন যুগের নিদর্শন তাহা নিঃসংশয়ে বলা কঠিন। কারণ একই সময়ে বাংলায় বিভিন্ন আদর্শের শিল্প প্রচলিত ছিল, ইহা অসম্ভব নহে। বাংলায় গুপ্তরাজত্ব প্রতিষ্ঠার পর হইতেই গুপ্তশিল্পের প্রভাবও যে এদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল, এরূপ অনুমান করা যায়। তাঁহার ফলে একদল সম্পূর্ণভাবে এই নূতন আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিল, আর একদল নূতন আদর্শ কতকাংশে গ্রহণ করিলেও প্রাচীন পন্থা একেবারে ত্যাগ করে নাই। এই দুই দল এবং অবিকৃত প্রাচীনপন্থিগণ একই সময়ে বর্ত্তমান থাকিতে পারে এরূপ কল্পনা একেবারে অযৌক্তিক নহে।
.
গ। পোড়া-মাটির শিল্প
প্রাচীন বাংলায় পোড়ামাটির শিল্প খুবই উন্নতি লাভ করিয়াছিল। পাহাড়পুর ব্যতীত আরও অনেক স্থানে, বিশেষত কুমিল্লার নিকটবর্ত্তী ময়নামতী ও লালমাই পৰ্ব্বতে, অনেকগুলি পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে কিন্নর (চিত্র নং ১০ ক), বিদ্যাধর (১৩ খ), বিবিধ ভঙ্গীর নারীমূৰ্ত্তি (১০ খ-গ, ১৩ গ-ঘ), অসি ও বর্শ্বহস্তে সৈনিক (১২ ক), ব্যাঘ্ৰ শিকারী (১২ খ), ব্যায়ামকারী (১১ ক), পদ্ম (১১ খ), নানারূপ প্রকৃত ও কাল্পনিক জন্তু ও দেব-দেবীর মূর্ত্তি প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার অধিকাংশই পাহাড়পুরের প্রথম শ্রেণীর ন্যায় লোকশিল্পের নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কিন্তু কয়েকটি রচনাভঙ্গি অপেক্ষাকৃত উচ্চাঙ্গের শিল্পজ্ঞানের পরিচায়ক (১০ খ-গ)। ইহাছাড়া অনেক খোদিত ইটও পাওয়া গিয়াছে।
প্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরীর ধ্বংসের মধ্যেও বহু পোড়ামাটির ফলক ও মূর্ত্তি এবং কারুকাৰ্য্য-খোদিত ইট পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে গোবিন্দ-ভিটায় প্রাপ্ত একটি গোলাকৃতি ফলক অথবা চক্রকে খোদিত মিথুনমূৰ্ত্তি (১৫ খ) উৎকৃষ্ট শিল্পকলার নিদর্শন।
বাংলায় প্রস্তর খুব সুলভ না হওয়ায় মৃৎশিল্প খুব বেশী জনপ্রিয় ছিল এবং লোকশিল্প হিসেবে পালযুগে, এবং সম্ভবত তাঁহার বহু পূৰ্ব্বেও, বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। মধ্যযুগেও বাংলার এই জাতীয় শিল্পপ্রতিভার কিছু কিছু নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।
.
ঘ। পালযুগের শিল্প
নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ-এই চারি শতাব্দের শিল্পকে পালযুগের শিল্প নামে অভিহিত করা যাইতে পারে। কারণ যদিও দ্বাদশ শতাব্দে সেনরাজগণ বাংলায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল এবং বৰ্ম্ম, চন্দ্র প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজবংশও এই যুগে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছেন, তথাপি এই চারি শতাব্দের শিল্প মোটামুটি একই লক্ষণাক্রান্ত এবং পালরাজ্যেই ইহার অভ্যুদয় ও বিকাশ ঘটিয়াছিল।
এই যুগের প্রস্তর ও ধাতুশিল্পের যে সমুদয় নিদর্শন এযাবৎ পাওয়া গিয়াছে, তাঁহার বিষয়বস্তু কেবলমাত্র দেব-দেবীর মূর্ত্তি। বাস্তব সংসার ও সমাজের সহিত ইহার প্রত্যক্ষ কোনো সম্বন্ধ নাই। বিভিন্ন ধর্ম্মগ্রন্থে দেব-দেবীর যে ধ্যান আছে সৰ্ব্বতোভাবে তাঁহার অনুসরণ করিয়া শিল্পীকে এই সমুদয় নিৰ্মাণ করিতে হইত। সুতরাং শাস্ত্রের অনুশাসন নিগড়পাশের ন্যায় শিল্পীর স্বাধীন ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত করিত। শিল্পী বা শিল্পের কোনো অব্যাহত গতি ছিল না। প্রকৃত শিল্প মূর্ত্তির মধ্য দিয়ে তাঁহার কলানৈপুণ্য ও সৌন্দৰ্য্যবোধ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছে ইহাই তাঁহার কৃতিত্ব।
উপকরণ বিষয়েও শিল্পীর খুব স্বাধীনতা ছিল না। অষ্টধাতু ও কালো কষ্টিপাথর, সাধারণত ইহাই ছিল মূর্ত্তি নির্মাণের প্রধান উপাদান। রৌপ্য এবং স্বর্ণও মূর্ত্তি নির্মাণে ব্যবহৃত হইত, কিন্তু এরূপ মূর্ত্তির সংখ্যা খুবই কম। কাষ্ঠনির্ম্মিত মূর্ত্তিও মাত্র কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে।
পালযুগের চারিশত বৎসরে শিল্পের অনেক বিবর্ত্তন হইয়াছিল। কিন্তু এই বিবর্ত্তনের ইতিহাস সঠিকরূপে জানিবার উপায় নাই। অধিকাংশ মূৰ্ত্তিরই নির্মাণকাল মোটামুটিভাবেও জানা যায় না। এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত বহু শত মূর্ত্তির মধ্যে মাত্র পাঁচখানিতে সময়বিজ্ঞাপক লিপি উৎকীর্ণ আছে। ইহার মধ্যে একখানি দশ, দুইখানি একাদশ ও দুইখানি দ্বাদশ শতাব্দের। কোনো এক শতাব্দীর মাত্র একখানি বা দুইখানি মূর্ত্তির সাহায্যে সেই শতাব্দীর বিশিষ্ট শিল্প-লক্ষণ স্থির করা দুঃসাধ্য। সুতরাং কেবলমাত্র শিল্পের ক্রমগতির সাধারণ রীতির দিক দিয়া বিচার করা ছাড়া বাংলার এই যুগের শিল্পবিবর্ত্তনের ইতিহাস জানিবার আর কোনো উপায় নাই। কিন্তু এই সাধারণ রীতিগুলি যথাযথভাবে স্থির করা সহজ নহে, এবং অনেক সময়ে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব ও অন্য অনেক বিশিষ্ট কারণে সাধারণ রীতির ব্যতিক্রম বা বিপর্যয় ঘটে। সুতরাং কেবলমাত্র এই রীতি অবলম্বনে রচিত বিবর্ত্তনের ইতিহাস সৰ্ব্বথা নির্ভরযোগ্য নহে। বাংলার শিল্প সম্বন্ধে এইরূপ ইতিহাস রচনার চেষ্টা খুব বেশি হয় নাই। যে দুই-একজন করিয়াছেন তাহাদের মতামত খুব স্পষ্ট নহে এবং সর্ব্বসাধারণে গৃহীত হয় নাই।
রচনাবিন্যাস, গঠনপ্রণালী ও সৌন্দৰ্য্য বিকাশের দিক দিয়া বিচার করিলে এই সমুদয় মূর্ত্তির মধ্যে অনেক শ্রেণীভেদ করা যায়। কিন্তু এই সমুদয় প্রভেদ কতটা স্থান বা কালের প্রভাবে এবং কতটা শিল্পীর ব্যক্তিগত রুচি বা অন্য কোনো কারণে ঘটিয়াছে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এই সমুদয় কারণে কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্ত সম্ভব না হইলেও বাংলার এ যুগের ইতিহাস আলোচনা করিতে গিয়া অনেকেই শিল্প বিবর্ত্তনের দুই-একটি মূলসূত্র অবলম্বন করিয়াছেন। বিবর্ত্তনের দিক দিয়া মূল্য খুব বেশী না হইলেও বিশ্লেষণের দিক হইতে এইগুলি ইতিহাস আলোচনায় প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই।
সাধারণত মূৰ্ত্তিগুলি একটি বড় প্রস্তরখণ্ডের মধ্যস্থল হইতে কাটিয়া বাহির করা হয়। মূল মূর্ত্তিটি কেন্দ্রস্থলে এবং পারিপার্শ্বিক মূৰ্ত্তিগুলি ও বিভূষণাদি এবং চালচিত্র ইহার দুই পার্শ্বে ও উপরে থাকে। প্রথমে মূৰ্ত্তিগুলির গভীরতার এক অৰ্দ্ধ মাত্র পাষাণের উপর উত্তীর্ণ হইত, কিন্তু ক্রমেই এই গভীরতার মাত্রা বৃদ্ধি হয়। পরিশেষে মূল মূর্ত্তিটি প্রায় সম্পূর্ণ আকার লাভ করে এবং এই উদ্দেশ্যে ইহার চতুম্পার্শ্বস্থ পাথর কতকটা একেবারে কাটিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। আবার প্রথম প্রথম মূল মূর্ত্তিটিই শিল্পীর প্রধান লক্ষ্য থাকে ও দর্শকের প্রায় সমগ্র মনোযোগ আকৃষ্ট করে। ক্রমশ পারিপার্শ্বিক মূর্ত্তিগুলি ও নানাবিধ কারুকার্যে বিভূষিত চালচিত্র অধিকতর প্রাধান্য লাভ করে এবং সুদক্ষ শিল্পীর হস্তে মূল মূর্ত্তির শোভাবর্দ্ধন করে। কিন্তু সর্বশেষ কোনো কোনো স্থলে এইসব পারিপার্শ্বিক মূর্ত্তি ও অলঙ্কারের প্ৰাচুৰ্য্য এত বৃদ্ধি পায় যে মূল মূর্ত্তিটিই অপ্রধান হইয়া পড়ে। অনেকেই মনে করেন যে এই দুইটি পরিবর্ত্তনই খুব সম্ভব প্রধানত কালপ্রবাহের ফলে ঘটিয়াছে; অর্থাৎ উত্তীর্ণ মূৰ্ত্তির অতিরিক্ত গভীরতা এবং পারিপার্শ্বিক মূর্ত্তি ও চালচিত্রে অলঙ্কারের অতিরিক্ত ও অযথা বাহুল্য শিল্পীর অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীনতার প্রমাণ। কিন্তু ইহা যে একটি সাধারণ সূত্র হিসেবে গ্রহণ করা যায় না, রাজা গোবিন্দচন্দ্রের নামাঙ্কিত লিপিযুদ্ধ বিষ্ণু ও সূৰ্য্যমূৰ্ত্তির সহিত রাজা তৃতীয় গোপালের চতুর্দ্দশ বৎসরে উত্তীর্ণ সদাশিব-মূৰ্ত্তির তুলনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।
একজন প্রসিদ্ধ শিল্পসমালোচক বাংলার এই যুগের শিল্প-বিবর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শতাব্দের শিল্পের লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে নবম শতাব্দে দেহের কমনীয়তা, সুডৌল গঠন ও শান্ত সমাহিত মুখশ্রী; দশমে শক্তিব্যঞ্জক দৃঢ় বলিষ্ঠ দেহ; একাদশে ক্ষীণ তনু, সুকোমল ভাবপ্রবণতা, মুখমণ্ডলের অপার্থিব দিব্যভাব ও দেহের ঊৰ্দ্ধভাগের লাবণ্য ও সুষমা; এবং দ্বাদশে ভাবব্যঞ্জনাহীন মুখশ্রী, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কৃত্রিম আড়ষ্টতা ও বসন ভূষণের প্রাচুর্য্য;-ইহাই এই চারি যুগের বাংলার শিল্পের প্রধান লক্ষণ। নিছক শিল্পের হিসাবে বাংলার মূর্ত্তিগুলিকে মোটামুটি এইরূপভাবে শ্রেণীবদ্ধ করা সম্ভবপর, কিন্তু এই চারিটি শ্রেণী যে পর পর চারিটি শব্দের প্রতীক, এই মত গ্রহণ করা কঠিন। পূর্ব্বোক্ত গোবিন্দচন্দ্র ও তৃতীয় গোপালের সময়কার মূর্ত্তির তুলনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। প্রথম মহীপাল ও গোবিন্দচন্দ্র সমসাময়িক। কিন্তু এই দুই রাজার নামাঙ্কিত লিপিযুক্ত দুইটি বিষ্ণুমূর্ত্তি উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগে এক পর্যায়ে পড়ে না।
কালানুযায়ী বিশ্লেষণ সম্ভবপর না হইলেও, পালযুগের শিল্প সম্বন্ধে সাধারণভাবে কয়েকটি সিদ্ধান্ত করা যায়। শিল্পীগণ পাথরের বা ধাতুর উপর খোদাই করিতে যে অসাধারণ দক্ষতা লাভ করিয়াছিল, তাহাতে কোনো সন্দেহ নাই। লতা, পাতা, জীব, জন্তু ও নানারূপ নকশার কাজ অনেক মূর্ত্তিতে এমন নিপুণ ও সূক্ষ্মভাবে সম্পাদিত হইয়াছে যে, বহুবর্ষব্যাপী শিক্ষা ও সাধনা এবং পুরুষানুক্রমিক অভ্যাস ব্যতীত ইহা কদাচ সম্ভবপর হইত না। এই যুগের মূৰ্ত্তিগুলি যত্নপূৰ্ব্বক পরীক্ষা করিলে বাংলার লুপ্ত চারুশিল্প সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা করা যায় এবং বাংলা দেশে যে অন্তত পাঁচ-ছয়শত বৎসর একটি জীবন্ত ও উচ্চাঙ্গের শিল্পধারা অব্যাহতভাবে প্রবাহিত ছিল, ইহাতে কোনো সন্দেহ থাকে না।
মনুষ্যমূর্ত্তিগঠনই ভাস্কৰ্য্যশিল্পের উৎকর্ষের সর্বশ্রেষ্ট পরিচয় ও প্রমাণ। বাংলার শিল্পী এ বিষয়ে কতটা সফলতা লাভ করিয়াছিল, তাঁহার বিচার করিতে হইলে বাংলার দেব-দেবীমূৰ্ত্তিই আমাদের একমাত্র অবলম্বন। ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির নিকট দেব-দেবীর মূৰ্ত্তি মাত্রেই সুন্দর। রাধাকৃষ্ণের নামসম্বলিত কবিতা ও সংগীত মাত্রেই যেমন একশ্রেণীর লোককে মুগ্ধ করে, দেব-দেবীর যেকোনো চিত্র বা মূৰ্ত্তিই তেমনি অনেকের নিকট অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের আকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়; এমনকি কালীঘাটের পটের ছবিও কেহ কেহ উচ্ছ্বসিত ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা ভক্তের দৃষ্টি, শিল্পের অনুভূতি নহে। শিল্পের প্রকৃত বিচার করিতে হইলে, তাহা কেবল ভাব ও সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তির দিক দিয়াই করিতে হইবে। দেব-দেবীর মূর্ত্তিই যে আমাদের অতীত ভাস্কৰ্য্যশিল্পের একমাত্র নিদর্শন, ইহা এই শিল্পের প্রকৃত ইতিহাস জানিবার একটি অন্তরায়। কিন্তু এই অন্তরায় অগ্রাহ্য বা অস্বীকার না করিয়া ইহার সাহায্যেই যত দূর সম্ভব শিল্পের পরিচয় দিতে হইবে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও দেব-দেবীর মূর্ত্তির মধ্য দিয়েই শিল্পের বিকাশ হইয়াছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইউরোপীয় শিল্পীগণও দেব-দেবীর মূৰ্ত্তির মধ্য দিয়াই অনবদ্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি করিয়া জগতে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। প্রাচীনযুগের ‘ভেনাস ডি মিলো এবং মধ্যযুগের র্যাফেল ও টিসিয়ান অঙ্কিত ম্যাডোনা ও ভেনাসের মূর্ত্তি দেবীরূপে কল্পিত হইলেও, ভাব ও সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তির জন্যই ইহা শিল্পজগতে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে।
সারনাথে গুপ্তযুগের যে সমুদয় মূর্ত্তি আছে, পালযুগের শিল্পে তাঁহার প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে অনেক গুরুতর প্রভেদ আছে। প্রথমত, গুপ্তযুগের সাবলীল স্বচ্ছন্দ ভঙ্গীর পরিবর্তে বাংলার মূর্ত্তিগুলির কতকটা আড়ষ্টভাব ও জড়তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। দ্বিতীয়ত, গুপ্তযুগের মূর্ত্তিতে একটি আত্মনিহিত অতীন্দ্রিয় ভাবের অভিব্যক্তিই শিল্পীর প্রধান লক্ষ্য, দেহের সুষমা ও লাবণ্য অপ্রধান ও এই ভাবেরই দ্যোতক মাত্র। বাংলার মূর্ত্তিগুলিতে এই আধ্যাত্মিক ভাব অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আনন্দ ও ভোগের ছবিই যেন বেশী করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। একের আদর্শ শান্ত-সমাহিত অন্তদৃষ্টি, অন্যের আদর্শ কান্ত ও কমনীয় বাহ্য রূপ। বাংলার মূর্ত্তিতে যে আধ্যাত্মিক ভাবের বিকাশ নাই তাহা নহে, কিন্তু তাঁহার প্রকাশভঙ্গীতে সাধারণত অন্তরের সংযম অপেক্ষা ভাবপ্রবণতার উচ্ছ্বাসই বেশী বলিয়া মনে হয়। তবে পালযুগের শ্রেষ্ঠ মূর্ত্তিগুলিতে এই দুই আদর্শের সমন্বয় দেখিতে পাওয়া যায়। এই মূর্ত্তিগুলি “কোমল অথচ সংযত, ভাবপ্রবণ অথচ ধ্যানস্থ, লীলায়িত অথচ দৃঢ়প্রতিষ্ঠ।” বাংলার শিল্প গুপ্তযুগের শিল্পের অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইলেও, সমসাময়িক পশ্চিম, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের শিল্প অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ এই সমুদয় শিল্পে সাধারণত গুপ্তযুগের আধ্যাত্মিক ভাব এবং পালযুগের সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য উভয়েরই অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে মধ্যযুগের এই মূর্ত্তিগুলি প্রাণহীন ও অসুন্দর, এবং ধর্ম্মমত ও ধৰ্ম্মানুষ্ঠানের পাষাণময় রূপ ব্যতীত শিল্প হিসাবে ইহার বিশেষ কোনো সার্থকতা নাই। অবশ্য কদাচিৎ এই সমুদয় অঞ্চলেও সুন্দর মূর্ত্তি দেখা যায়,-দৃষ্টান্ত স্বরূপ এলিফান্টা দ্বীপের মূর্ত্তিগুলির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণত এই সমুদয় দেশে মধ্যযুগের মূর্ত্তিগুলি শ্রীহীন। কেবল বিহারে ও উড়িষ্যায় বাংলার ন্যায় সৌন্দর্য্যের আদর্শ শিল্পে বর্ত্তমান দেখা যায়। বাংলার পালযুগের শিল্পের প্রভাব এই দুই প্রদেশে এমনকি যবদ্বীপ ও পূৰ্ব্ব ও ভারতীয় অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জে বিস্তৃত হইয়াছিল।
এ পর্য্যন্ত যে সমুদয় আলোচনা করা হইয়াছে তাহা এই যুগের শিল্প সম্বন্ধে সাধারণভাবে প্রযোজ্য। কোনো কোনো মূর্ত্তিতে যে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যাইবে তাহা বলাই বাহুল্য, কারণ কোনো দেশের অথবা কোনো যুগের শিল্পই কয়েকটি সাধারণ নিয়মের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। পালযুগের শিল্প সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে হইলে এই যুগের মূর্ত্তির সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় আবশ্যক। বর্ত্তমান গ্রন্থে মূর্ত্তিগুলির বিস্তৃত বিবরণ বা আলোচনা সম্ভবপর নহে বলিয়াই আমরা সংক্ষেপে এই যুগের শিল্পের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য করিয়াছি। এই সকল মন্তব্য বিশদ ও পরিস্ফুট করিবার জন্য কয়েকটি মূর্ত্তির উল্লেখ করিতেছি।
শিল্পের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বিষ্ণু ও তাঁহার পারিপার্শ্বিক দেব-দেবীর মূৰ্ত্তিগুলিই প্রাধান্য লাভ করে। শিয়ালদির বিষ্ণুমূর্ত্তির মুখে শিল্পী বেশ একটু নূতনত্ব ও বৈশিষ্ট্য ফুটাইয়াছেন। বিষ্ণুর উপরের দুই হস্তের অঙ্গুলির বক্রভাব কোমলতা ও কমনীয়তার সূচক, যদিও চক্র ও গদা এই দুই সংহারকারী অস্ত্র ধরিবার সহিত তাঁহার সামঞ্জস্য নাই। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, দুই স্তম্ভের ন্যায় সমান্তরাল পদযুগলের উপর দণ্ডায়মান সরল রেখার ন্যায় দেহগঠন শিল্পীর কৌশলের অভাব নহে, কঠোর নিয়মানুবর্তিতাই সূচিত করে। পার্শ্বচারিণী দুইজনের বঙ্কিম দেহভঙ্গী হইতেও ইহা প্রমাণিত হয়। এই দুই পার্শ্বচারিণীর মূৰ্ত্তি লাবণ্য ও সুষমার সহিত গাম্ভীৰ্য্য ও ভক্তির সংমিশ্রণে অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে। বজ্রযোগিনীর মৎস্যাবতার মূর্ত্তিতে (চিত্র নং ২০) বিষ্ণুর মুখের কমনীয় কান্তি, অধর-যুগলের হাসিরেখা ও দেহের সুডৌল গঠন এমন কৌশলে সম্পাদিত হইয়াছে যে, বিষ্ণুর অধোভাগ মৎস্যের আকার হইলেও এই অসঙ্গতি শিল্পের সৌন্দর্য্যের হানি করে নাই। বাঘাউরার প্রস্তরনির্ম্মিত (চিত্র নং ১৮) এবং সাগরদীঘি, রঙ্গপুর ও বগুড়ার ধাতুনির্ম্মিত বিষ্ণুমূৰ্ত্তি (চিত্র নং ২১ ঘ, ১৯) উচ্চশ্রেণীর শিল্পকলার নিদর্শন। মূর্ত্তিগুলির কৃত্রিম দাঁড়াইবার ভঙ্গীর সহিত পার্শ্বচারিণীগণের সহজ সাবলীল ভাব বিশেষভাবে তুলনীয়। দেওরা ও বাণগড়ের বিষ্ণুমূর্ত্তিও উচ্চাঙ্গের শিল্পকলার নিদর্শন। মুর্শিবাবাদ জিলার অন্তর্গত ঝিল্লির বরাহ অবতারের মূৰ্ত্তিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মূৰ্ত্তির মুখ বরাহের হইলেও, মনুষ্যাকৃতি অধোভাগে শিল্পী অনবদ্য সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। বিক্রমপুর ও বীরভূমের অন্তর্গত পাইকোরে প্রাপ্ত দুইটি নরসিংহমূৰ্ত্তিও কেবলমাত্র দেহসৌষ্ঠবে উচ্চশ্রেণীর শিল্পে পরিণত হইয়াছে।
বাঘরার বলরামমূর্ত্তির মুখে শিল্পী একটি স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ছাপ দিয়াছেন। ইহার সরল অনাড়ম্বর পশ্চাদপটে মূল মূর্ত্তি এবং তাঁহার পার্শ্বচারিণী ও বাহনের মূর্ত্তি কয়টির সৌন্দৰ্য্য উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। ছাতিন গ্রামের সরস্বতী মূৰ্ত্তির (চিত্র নং ২৩) অঙ্গসৌষ্ঠব, বসিবার ভঙ্গী ও অপূৰ্ব্ব মুখশ্রী, এবং তাঁহার পারিপার্শ্বিক মূর্ত্তি ও বিভূষণাদি উচ্চশ্রেণীর শিল্পের পরিচায়ক। নাগইল ও বিক্রমপুরে প্রাপ্ত দুইটি এবং কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত (চিত্র নং ২৭ গ) গরুড়মূৰ্ত্তিতে শিল্পী যে দাস্য ও ভক্তির মাধুৰ্য্য প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক।
শিবমূৰ্ত্তির মধ্যে শঙ্করবাঁধার নটরাজ শিবের মূৰ্ত্তি (চিত্র নং ২২ গ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিবের তাণ্ডবনৃত্যের সহিত উর্দ্ধমুখ বৃষেরা উচ্ছ্বসিত নৃত্য শিল্পীর অপূৰ্ব্ব সৃজনশক্তির পরিচায়ক। নৃত্যের গতিভঙ্গী ও উদ্দামতা এই মূর্ত্তির মধ্য দিয়া অপরূপ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। বরিশালে প্রাপ্ত ব্রঞ্জের শিবমূৰ্ত্তিতে (চিত্র নং ২৮ খ) শিল্পী একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের ছাপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন এবং ধাতুমূৰ্ত্তির নিৰ্মাণকৌশল কত দূর উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাঁহার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। গণেশপুরে প্রস্ফুটিত পদ্মের স্বাভাবিক আকৃতিতে শিল্পী সূক্ষ্ম সৌন্দৰ্যানুভূতি ও স্বাতন্ত্রের পরিচয় দিয়াছেন। বাংলায় চলিত কথায় কার্তিকই সৌন্দর্য্যের আদর্শ। উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত একটি ময়ূরবাহন কার্তিকে (চিত্র নং ২১ ক) শিল্পী এই সৌন্দর্যের পরিচয় দিয়াছেন। শেষোক্ত দুইটি মূৰ্ত্তিতেই অলঙ্কারের বাহুল্য দেখা যায়। শিল্পীর কৌশলে ইহা মূৰ্ত্তিদ্বয়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছে, কিন্তু নিকৃষ্ট শিল্পীর হস্তে এইরূপ প্রাচুর্যে সৌন্দর্য্যের হানি হয়।
ঈশ্বরীপুরীর গঙ্গামূৰ্ত্তি বাংলার এই যুগের শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ইহার স্বাভাবিক লীলায়িত পদক্ষেপ ও বিশিষ্ট মুখশ্রী, এবং পার্শ্বচর মূর্ত্তি দুইটির সুন্দর সরল দেহভঙ্গী সমগ্র মূর্ত্তিটিকে অপরূপ সুষমা প্রদান করিয়াছে।
রাজসাহীর ইন্দ্রাণী (চিত্র নং ২২খ), বিক্রমপুরের মহাপতিসরা (চিত্র নং ২১ গ) এবং খালিকৈরের বৌদ্ধ তারাও (চিত্র নং ১৩ ক) এই শ্রেণীর সুন্দর মূর্ত্তি। কঠিন পাথরের মধ্য দিয়ে রক্তমাংসের দেহের কমনীয়তা ও নমনীয়তা ফুটিয়া উঠিয়াছে।
বাংলায় অনেকগুলি সূর্যমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে কয়েকখানিতে উচ্চাঙ্গ ও বিশিষ্ট শিল্পজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। যাত্রাপুরের সূর্যের মুখশ্রী (চিত্র নং ১৬ ক) এবং কোটালিপাড়া (চিত্র নং ১৭) ও চন্দ্রগ্রামের (চিত্র নং ১৬ খ) সূৰ্য্যমূর্ত্তির রচনা-বিন্যাস ও শান্ত-সমাহিত ভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
বিহারৈলের বুদ্ধমূর্ত্তিতে বাংলার যে শিল্পধারার সূচনা দেখা যায়, পালযুগে তাঁহার কিরূপ বিকাশ হইয়াছিল, ঝেওয়ারিতে প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্ত্তি (চিত্র নং ২৪) তাঁহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কিন্তু, সম্ভবত ব্ৰহ্মদেশের প্রভাবে, বুদ্ধমূর্ত্তির পরিকল্পনা কিরূপ পরিবর্তিত হইয়াছিল, ঝেওয়ারির আর একটি বুদ্ধমূৰ্ত্তি (চিত্র নং ২৫) হইতে তাহা জানা যায়। প্রাচীন মগধের শিল্পধারার সহিত বাংলার শিল্পী কিরূপ সুপরিচিত ছিল, শিববাটির বুদ্ধমূৰ্ত্তি (চিত্র নং ২৭ খ) তাঁহার চমৎকার দৃষ্টান্ত। বুদ্ধ শান্ত সমাহিতভাবে মন্দির-মধ্যে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় উপবিষ্ট এবং তাঁহার চতুস্পার্শ্বে তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী পৃথক পৃথক ক্ষুদ্র আকারে উৎকীর্ণ। গুপ্তযুগের সারনাথ শিল্পের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইলেও এইরূপ রচনাপ্রণালী মগধ ও বঙ্গের একটি বিশিষ্ট শিল্পকৌশল বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য।
কিন্তু কোনো কোনো বুদ্ধমূৰ্ত্তিতে এই সমুদয় বিদেশীয় প্রভাব বর্ত্তমান থাকিলেও বাংলার শিল্পী অনেক সময়ই বাংলার নিজস্ব শিল্পধারা অব্যাহত রাখিয়া সুন্দর বুদ্ধমূৰ্ত্তি গড়িয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত অবলোকিতেশ্বর (চিত্র নং ২১ খ) এবং ময়নামতীতে প্রাপ্ত মঞ্জুর বোধিসত্ত্বের (চিত্র নং ১৪) উল্লেখ করা যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত খালিকৈরের তারামূৰ্ত্তির (চিত্র নং ১৩ ক) ন্যায় এই দুইখানির অনবদ্য মুখশ্রী, সাবলীল দেহভঙ্গী ও রচনাবিন্যাস উৎকৃষ্ট শিল্পের নিদর্শন।
.
৩. চিত্রশিল্প
পালযুগের পূর্ব্বেকার কোনো চিত্র অদ্যাবধি বাংলায় আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু খুব প্রাচীনকাল হইতেই যে এদেশে চিত্রাঙ্কনের চর্চ্চা ছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। ফাহিয়ান তাম্রলিপ্তির বৌদ্ধবিহারে অবস্থানকালে বৌদ্ধমূর্ত্তির ছবি আঁকতেন। সুতরাং তখন তাম্রলিপ্তিতে যে চিত্রশিল্প পুরাতন ও সুপরিচিত ছিল, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।
সাধারণ মন্দির ও বৌদ্ধবিহার প্রভৃতির প্রাচীরগাত্র চিত্র দ্বারা শোভিত হইত। পরবর্ত্তীকালের শিল্পশাস্ত্রে স্পষ্ট এইরূপ অনুশাসন আছে এবং ভারতের অনেক স্থানে ইহার চিহ্ন এখনো বর্ত্তমান আছে। বাংলার অনেক মন্দির ও বিহারে সম্ভবত বহু চিত্র ছিল, মন্দির ও বিহারের সঙ্গেই তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।
একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দে লিখিত কয়েকখানি বৌদ্ধ গ্রহের পুঁথিতে অঙ্কিত বজ্রযান-তন্ত্রযান মতোক্ত দেব-দেবীর ছবি ব্যতীত প্রাচীন বাংলার আর কোনো ছবি এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ইহার মধ্যে রামপালের রাজত্বের ৩৯শ বর্ষে ও হরিবর্ম্মার ১৯শ বর্ষে লিখিত দুইখানি অষ্টসাহস্রিকা-এবং হরিবর্ম্মার ৮ম বর্ষে লিখিত একখানি পঞ্চবিংশতিসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথি বাংলার প্রাচীন চিত্রবিদ্যা আলোচনার প্রধান অবলম্বন।
রেখাবিন্যাস ও বর্ণসমাবেশ এই দুয়ের উপরই চিত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং এ দুয়ের প্রাধান্য অনুসারেই চিত্রের দুইটি প্রধান শ্রেণীবিভাগ কল্পিত হইয়াছে। অজন্তা ও এলোরার চিত্রশিল্পে এই দুই শ্রেণীরই চিত্র দেখা যায়, এবং পরবর্ত্তীকালে ভারতের সর্বত্রই ইহার প্রভার পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিম ভারতবর্ষের চিত্রে রেখাবিন্যাসই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, কিন্তু বাংলার চিত্রে বর্ণসমাবেশ ও রেখাবিন্যাস উভয়েরই প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। পশ্চিম ভারতের চিত্রের সহিত তুলনা করিলে ইহাও বুঝা যায় যে, বাংলার শিল্পী রেখাবিন্যাসে অধিকতর দক্ষতা দেখাইয়াছেন এবং ইহার সাহায্যে যে সৌন্দর্য্য ও মাধুর্যের অবতারণা করিয়াছেন, পশ্চিম ভারতের চিত্রে তাহা দুর্লভ। বাংলার এই চিত্রশিল্পের প্রভাব আসাম, নেপাল ও ব্রহ্মদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল।
পরিকল্পনার দিক দিয়া বাংলার চিত্র ও প্রস্তরে উত্তীর্ণ মূর্ত্তির মধ্যে প্রভেদ বড় বেশী নাই। উভয়েরই বিষয়বস্তু ও রচনাপদ্ধতি, এমনকি ভঙ্গী ও অঙ্গসৌষ্ঠব, প্রায় একই প্রকারের। কেন্দ্রস্থলে মূল দেব-দেবী, এবং দুই পার্শ্বে আনুষঙ্গিক মূর্ত্তিগুলি ও কদাচিৎ অলঙ্কাররূপে ব্যবহৃত দৃশ্যাবলী। কেবল দুই-এক স্থলে মূল মূর্ত্তিটি এক পার্শ্বে উপবিষ্ট। এইসব চিত্রে প্রায় এক অর্ধে কেবল মূল মূর্ত্তিটি এবং অপর অর্ধে অন্য সব পারিপার্শ্বিক মূর্ত্তিগুলির সমাবেশ করিয়া মূল মূর্ত্তির প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে।
রাজা রামপালের রাজত্বের ৩৯শ বর্ষে লিখিত অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতার পুঁথিখানিতে যে কয়েকটি ছবি আছে, তাহা বাংলার চিত্রশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। সাধারণ কয়েকটি বর্ণ এবং সূক্ষ্ম রেখাপাতের সাহায্যে শিল্পী এই সমুদয় চিত্রের মধ্যে একটি লীলায়িত মাধুৰ্য্য ও অনবদ্য সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়া মধ্যযুগের শিল্পজগতে উচ্চস্থান অধিকারের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছেন। বাংলার চিত্রশিল্পের নমুনা মুষ্টিমেয় হইলেও, ইহা যে স্বর্ণমুষ্টি তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।
কেবলমাত্র রেখার সাহায্যে চিত্র-অঙ্কনে বাংলার শিল্পী কত দূর পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, সুন্দরবনে প্রাপ্ত ডোম্মনপালের তাম্রশাসনের অপর পৃষ্ঠে উৎকীর্ণ বিষ্ণুর রেখাচিত্র তাঁহার দৃষ্টান্ত। প্রাচীন বাংলার তাম্রপটে উৎকীর্ণ এইরূপ আরও দুইটি রেখাচিত্র পাওয়া গিয়াছে।
.
৪. বাংলার শিল্পী
বাংলার শিল্পীগণের সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই জানি না। তিব্বতীয় লামা তারনাথ লিখিয়াছেন যে, ধীমান ও তাঁহার পুত্র বিৎপালো প্রস্তর ও ধাতুর মূর্ত্তিগঠন এবং চিত্রাঙ্কনে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্যগণ একটি স্বতন্ত্র শিল্পী সম্প্রদায় গঠন করিয়াছিলেন। এই শিল্পীদ্বয়ের নির্ম্মিত কোনো মূৰ্ত্তি বা তাঁহাদের সম্বন্ধে অন্য কোনো বিবরণ পাওয়া যায় নাই। কিন্তু বাংলায় যে শিল্পীসংঘ ছিল, বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তিতে তাঁহার উল্লেখ আছে। ইহার ৩২টি অতিবৃহৎ পংক্তির অক্ষরগুলি যেরূপ সুন্দরভাবে পাথরে খোদিত হইয়াছে, তাহা উৎকৃষ্ট শিল্পকাৰ্য্য বলিয়া গণ্য করা যায়। যে শিল্পী ইহা উত্তীর্ণ করিয়াছিলেন, প্রশস্তির শেষ শ্লোকে তাঁহার পরিচয় আছে। তিনি ধর্ম্মের প্রপৌত্র, মনদাসের পৌত্র, বৃহস্পতিবার পুত্র, বরেন্দ্রের শিল্পীগোষ্ঠী-চূড়ামণি রাণক শূলপাণি। ইহা ইহতে অনুমিত হয় যে, বরেন্দ্রে (এবং সম্ভবত বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে) একটি শিল্পীসংঘ ছিল এবং শূলপাণি এই সংঘের প্রধান ছিলেন। রাণক এই উপাধি হইতে মনে হয় যে, তিনি রাজ্যের একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। কিন্তু ভট্টভবদেবের প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ’ গ্রন্থ অনুসারে নৰ্ত্তক, তক্ষক, চিত্রোপজীবী, শিল্পী, রঙ্গোপজীবী, স্বর্ণকার ও কর্ম্মকার সমাজে হেয় বলিয়া পরিগণিত হইতেন, এবং কোনো ব্রাহ্মণ এই সমুদয় বৃত্তি অবলম্বন করিলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত। শূলপাণি সম্ভবত বংশানুক্রমে শিল্পীর কাৰ্য্য করিতেন। প্রস্তরে অক্ষর উত্তীর্ণ করাও যে প্রকৃত শিল্পীরই কাৰ্য্য ছিল, সিলিমপুরের প্রস্তরলিপির একটি শ্লোকে তাঁহার উল্লেখ আছে। এই লিপির উপসংহারে উক্ত হইয়াছে যে, প্রণয়ী যেমন তন্মনা হই বর্ণবিন্যাসে নিজের প্রণয়িনীর চিত্র অঙ্কিত করেন, শিল্পবিৎ সোমেশ্বর তেমনি এই প্রশস্তি লিখিয়াছিলেন। এই একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে শিল্পের প্রকৃতি ও অন্তর্নিহিত ভাবটি অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। গভীর অনুরাগ ও আসক্তিই যে শিল্পের প্রেরণা তাহা বাংলার শিল্পীগণ জানিতেন। বাংলার শিলালিপি ও তাম্রশাসন হইতে আমরা আরও কয়েকজন এইরূপ শিল্পীর নাম পাই যথা :
(১) ভোগটের পৌত্র, সুভটের পুত্র তাতট
(২-৩) সৎ-সমতট নিবাসী শুভ্রদাসের পুত্র মঙ্খদাস, ও তৎপুত্র বিমলদাস
(৪) সূত্রধর বিষ্ণুদ্র
(৫-৬) বিক্রমাদিত্য-পুত্র শিল্পী মহীধর ও তৎপুত্র শিল্পী শশীদেব
(৭) শিল্পী কর্ণভদ্র
(৮) শিল্পী তথাগতসার।
ইঁহাদের কয়েকজন স্পষ্টত শিল্পী উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। মোটের উপর এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, উল্লিখিত আটজন এবং শূলপাণি ও সোমেশ্বর প্রভৃতি যে কেবল প্রস্তর ও তাম্রপটে অক্ষর উৎকীর্ণ করিতেন তাহা নহে-তাহারা উচ্চশ্রেণীর শিল্পী ছিলেন এবং ধাতু ও প্রস্তরের মূর্ত্তি প্রভৃতিও গঠন করিতেন।
প্রস্তর ও ধাতুর মূৰ্ত্তিনির্মাণ ব্যয়সাপেক্ষ। সুতরাং অর্থশালী লোকই এই সমুদয় প্রতিষ্ঠা করিতেন। শিল্পীগণও এই সম্প্রদায়ের আদেশে এবং শাস্ত্রানুশাসন ও লোকাঁচারের নির্দেশমতো মূর্ত্তি প্রস্তুত করিতেন। ইহাতে তাহাদের শিল্পরচনার শক্তি ও স্বাধীনতা যে অনেক পরিমাণে খৰ্ব্ব হইত, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বিশেষত এই শিল্পীগণ যাঁহাদের অনুগ্রহে জীবিকা নির্বাহ করিতেন, শিল্পের সৌন্দৰ্যবোধ অপেক্ষা ধর্ম্মনিষ্ঠাই ছিল তাঁহাদের মনে অধিকতর প্রবল; সুতরাং বাংলার এই শিল্পীগণের পরিস্থিতি প্রকৃত শিল্পের উৎকর্ষের অনুকূল ছিল না। ইহা সত্ত্বেও তাহারা যে সূক্ষ্ম সৌন্দৰ্যবোধ ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁহাদের মধ্যে শিল্পের একটি সহজ ও স্বাভাবিক অনুভূতি ছিল। ধনী ও অভিজাতবর্গের অনুগ্রহে ও পৃষ্ঠপোষকতায় পরিপুষ্ট এই সমুদয় শিল্পীর রচনা সমাজের উচ্চশ্রেণীর মনোরঞ্জন ও প্রয়োজনের অনুকূল হইত। লোকশিল্পের যে দৃষ্টান্ত পাহাড়পুর, ময়নামতী, মহাস্থান প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়, পরবর্ত্তী যুগেও হয়তো তাহা ছিল, কিন্তু এযাবৎ তাঁহার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নাই।
২১. বাংলার বাহিরে বাঙ্গালী
একবিংশ পরিচ্ছেদ – বাংলার বাহিরে বাঙ্গালী
ভারতবাসীরা পূর্ব্ব এশিয়ায় ও পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যে বিপুল বাণিজ্য-ব্যবসায়, বহু-সংখ্যক রাজ্য ও উপনিবেশ স্থাপন, এবং হিন্দু-সভ্যতার বহুল প্রচার করিয়াছিল, তাঁহার মধ্যে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব কম ছিল না। এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। স্থলপথে ভারতবর্ষ হইতে ঐ সমুদয় দেশে যাইতে হইলে, বঙ্গদেশের মধ্য দিয়াই যাইতে হইত। আৰ্য্যাবৰ্ত্ত হইতে যাহারা জলপথে যাইতেন, তাঁহারও তাম্রলিপ্তি বন্দরেই জাহাজে উঠিতেন। এই সমুদয় কারণে এবং বঙ্গদেশের লোকেরা সৰ্ব্বাপেক্ষা নিকটে থাকায়, তাহাদের পক্ষেই এরূপ যাতায়াতের সুবিধা বেশী ছিল।
এই সিদ্ধান্ত কেবল অনুমানমূলক নহে। ইহার প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ব্রহ্মদেশের প্রাচীন স্থাপত্যশিল্প যে প্রধানত বাঙ্গালীরই সৃষ্টি, পণ্ডিতেরা তাহা একবাক্যে স্বীকার করেন। প্রাচীন ব্রহ্মদেশের এক অঞ্চল গৌড় নামে অভিহিত হইত। মালয় উপদ্বীপের এক শিলালিপি হইতে রক্তমৃত্তিকাবাসী বুদ্ধগুপ্ত নামক এক মহানাবিকের কথা জানা যায়; পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, এই রক্তমৃত্তিকা বা রাঙ্গামাটি বাংলায় অবস্থিত ছিল। শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজগণের গুরু ছিলেন একজন বাঙ্গালী, এবং যবদ্বীপে ও পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য দ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ও প্রসারে বাংলার যথেষ্ট প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। শৈলেন্দ্ররাজগণের সহিত পালসম্রাট দেবপালের যে সৌখ্য ছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। যবদ্বীপের কতকগুলি মূর্ত্তিতে উৎকীর্ণ লিপি তকালে বাংলা দেশে প্রচলিত অক্ষরে লিখিত। কাম্বোডিয়ার একখানি সংস্কৃত লিপিতে প্রাচীন গৌড়ীয় রীতির ছাপ এতই স্পষ্ট যে, কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে ইহার রচয়িতা হয় বাঙালি ছিলেন, নচেৎ বহুকাল বঙ্গদেশে থাকিয়া তথাকার সাহিত্যের অভিজ্ঞ হইয়াছিলেন। এই সমুদয় আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এশিয়ার পূর্ব্বখণ্ডে ভারতীয় রাজ্য ও সভ্যতা বিস্তারে বাঙ্গালীর প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে ছিল।
সিংহল-দ্বীপ বাঙ্গালী রাজকুমার বিজয় ও তাঁহার সঙ্গীগণ জয় করিয়াছিলেন, এই কাহিনী সিংহলদেশীয় গ্রন্থে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা কতদূর ঐতিহাসিক সত্য, তাহা বলা যায় না।
দুর্গম হিমালয়গিরি পার হইয়া বহু বৌদ্ধ আচাৰ্য ও পণ্ডিত তিব্বতে গিয়া তথাকার ধর্ম্মসংস্কারে সহায়তা করিয়াছিলেন। তিব্বতদেশীয় গ্রন্থে তাঁহাদের জীবনী ও বিস্তৃত বিবরণ আছে। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন বলিয়া মনে করিবার সঙ্গত কারণ আছে, তাহাদের কয়েকজনের বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি।
অষ্টম শতাব্দে তিব্বতের রাজা খৃস্রং-লদে-বসান গৌড়দেশীয় আচাৰ্য শান্তি রক্ষিতকে (অথবা শাস্ত্ররক্ষিত) তিব্বতে নিমন্ত্রণ করেন। শান্তিরক্ষিত নালন্দা মহাবিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি রাজনিমন্ত্রণে দুইবার তিব্বতে গমন করেন এবং তথাকার বৌদ্ধধর্ম্ম সংস্কার করেন। তাঁহার ভগ্নীপতি বৌদ্ধ আচার্য্য পদ্মসম্ভবও রাজনিমন্ত্রণে তিব্বতে গিয়া তাঁহার সাহায্য করেন। তিব্বতের রাজা হঁহাদের উপর খুব প্রসন্ন হন। তিনি মগধের ওদন্তপুরী বিহারের অনুকরণে রাজধানী লাসায় বসম য়া নামক একটি বিহার নির্মাণ করেন এবং শান্তিরক্ষিতকে ইহার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। শান্তিরক্ষিত ও পদ্মসম্ভব তিব্বতের বিখ্যাত লামা সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করেন এবং অনেক বৌদ্ধ গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঁহারা তিব্বতীয় ভিক্ষুকগণকে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত তথ্যগুলি যথাযথ শিক্ষা দিয়া তাঁহাদিগের দ্বারা দেশের নানা স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করান। শান্তিরক্ষিত ১৩ বৎসর উক্ত অধ্যক্ষের পদে ছিলেন। পরে তাঁহারই পরামর্শে তাঁহার শিষ্য কমলশীলকে তিব্বতের রাজা আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু কমলশীল তিব্বত পৌঁছিবার পূর্ব্বেই শান্তিরক্ষিতের মৃত্যু হয়। ইহার পূর্ব্বেই পদ্মসম্ভব তিব্বত ত্যাগ করিয়া অন্যান্য দেশে গিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করেন। কমলশীল তিব্বতে গুরুর আরব্ধ কাৰ্য্য সম্পন্ন করেন।
যে সকল বাঙ্গালী বৌদ্ধ আচার্য তিব্বতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সমধিক প্রসিদ্ধ। ইনি অতীশ নামেও সুপরিচিত এবং এখনো তিব্বতে তাঁহার স্মৃতি পূজিত হয়। তিব্বতীয় গ্রন্থে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। আমরা সংক্ষেপে তাঁহার বিবরণ দিতেছি।
বঙ্গল (বাংলা) দেশে বিক্রমণিপুরের গৌড়ের রাজবংশে ৯৮০ অব্দে দীপঙ্করের জন্ম হয়। বাল্যকালে তাঁহার নাম ছিল চন্দ্রগর্ভ। তাঁহার পিতার নাম কল্যাণশ্রী এবং মাতার নাম প্রভাবতী। তিনি প্রথমে জেরি ও পরে রাহুলগুপ্তের নিকট নানা বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। উনিশ বৎসর বয়সে তিনি ওদন্তপুরী বিহারে বৌদ্ধ-সম্ভের আচাৰ্য্য শীলরক্ষিতের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং গুরু তাঁহাকে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এই নাম দেন। এই সময় সুবর্ণদ্বীপের প্রধান ধর্ম্মাচাৰ্য্য চন্দ্রকীৰ্ত্তি বৌদ্ধজগতে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিবার মানসে দীপঙ্কর একখানি বাণিজ্য-জাহাজে কয়েক মাস সমুদ্রযাত্রা করিয়া সুবর্ণদ্বীপে উপস্থিত হন। সেখানে বারো বৎসর অধ্যয়ন করিয়া দীপঙ্কর সিংহল ভ্রমণ করিয়া মগধে গমন করেন। রাজা মহীপাল তাঁহাকে বিক্রমশীল বিহারে নিমন্ত্রণ করেন, এবং রাজা নয়পাল তাঁহাকে ইহার প্রধান আচাৰ্য্য পদে নিযুক্ত করেন। এই সময় তিব্বতের রাজা য়ে শেষ-হোড বৌদ্ধধর্ম্ম সংস্কার করিবার জন্য ভারতবর্ষ হইতে কয়েকজন আচার্য্য নিয়া যাইবার জন্য দুইজন রাজকর্ম্মচারী প্রেরণ করেন। ইহারা নানা দেশ ঘুরিয়া বিক্রমশীল বিহারে উপস্থিত হইলেন এবং ক্রমে জানিতে পারিলেন যে, দীপঙ্করই মগধের বৌদ্ধ আচাৰ্য্যদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু তিনি তিব্বতে যাইতে রাজী হইবেন না জানিয়া, তাঁহারা তিব্বতে ফিরিয়া গিয়া রাজার নিকট সমুদয় নিবেদন করিলেন। রাজা য়ে-শেষ-হোড় দীপঙ্করকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য মূল্যবান উপঢৌকনসহ কয়েকটি দূত পাঠাইলেন। দূতমুখে তিব্বতের রাজার প্রস্তাব শুনিয়া দীপঙ্কর যাইতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার স্বর্ণের কোনো প্রয়োজন নাই এবং খ্যাতি-প্রতিপত্তির জন্যও তিনি লালায়িত নহেন। রাজদূতগণ তিব্বতে প্রত্যাগমন করিবার অল্পকাল পরেই য়ে-শেষ-হেড এক সীমান্ত রাজার হস্তে বন্দী হইলেন। শত্ৰুকারাগারে তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি দীপঙ্করকে তিব্বতে যাইবার জন্য পুনরায় করুণ মিনতি জানাইয়া এক পত্র লেখেন। তিব্বতের নতুন রাজা চ্যান-চুর এই পত্রসহ কয়েকজন রাজদূত দীপঙ্করের নিকট প্রেরণ করেন। দীপঙ্কর ধর্ম্মপ্রাণ রাজার শোচনীয় মৃত্যুতে ব্যথিত হইয়া তাঁহার অন্তিম অনুরোধ পালনপূর্ব্বক তিব্বত গমনে স্বীকৃত হইলেন। নেপালের মধ্য দিয়া তিব্বতের সীমান্তে পৌঁছিলে রাজার সৈন্যদল তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিল। মানসসরোবরে এক সপ্তাহ কাটাইয়া তিনি সদলবলে থোলিং মঠে উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে রাজধানীতে পৌঁছিলে রাজা স্বয়ং মহাসমারোহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। অতঃপর তিব্বতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া তিনি বিশুদ্ধ মহাযান ধর্ম্ম প্রচার করেন এবং তথাকার বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার করেন। তিনি তেরো বৎসর তিব্বতে থাকিয়া প্রায় দুইশতখানি বৌদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। ১০৫৩ অব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে তিব্বতেই তাঁহার মৃত্যু হয়।
কেবল বিদেশে নহে, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও অনেক বাঙ্গালী জ্ঞানবীর ও কর্ম্মবীর যথেষ্ট কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন। বাংলার বাহিরে নালন্দা ও বিক্রমশীল এই দুই প্রসিদ্ধ বৌদ্ধবিহারে অনেক বাঙ্গালী আচাৰ্য খ্যাতি লাভ করিয়াছেন ও সর্বাধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন সাং যখন নালন্দায় যান, তখন বাংলার ব্রাহ্মণ-রাজবংশীয় শীলভদ্র এই মহাবিহারের প্রধান আচাৰ্য্য ও অধ্যক্ষ ছিলেন। হুয়েন সাংয়ের বিবরণ হইতে শীলভদ্রের জীবনী সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। শীলভদ্র ভারতের নানা স্থানে ঘুরিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি নালন্দায় ভিক্ষুপ্রবর ধর্ম্মপালের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহার নিকট দীক্ষা লাভ করেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দূরদেশেও বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সময় দাক্ষিণাত্যের একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মগধে আসিয়া ধর্ম্মপালকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেন। শীলভদ্রের বয়স তখন মাত্র ৩০ বৎসর, কিন্তু ধর্ম্মপাল তাঁহাকেই ব্রাহ্মণের সহিত তর্ক করিতে আদেশ দিলেন। শীলভদ্র ব্রাহ্মণকে পরাজিত করিলেন। মগধের রাজা ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া শীলভদ্রকে একটি নগরের রাজস্ব উপহার দিলেন। ভিক্ষুর ধনলোভ উচিত নহে-এই যুক্তি দেখাইয়া শীলভদ্র প্রথমে ইহা প্রত্যাখ্যান করিলেন, কিন্তু রাজার সনির্বন্ধ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তিনি এই দান গ্রহণ করিলেন এবং ইহার দ্বারা একটি বৌদ্ধবিহার প্রতিষ্ঠা করিলেন। কালক্রমে হুয়েন সাং ৬৩৭ অব্দে নালন্দায় গমন করেন। তখন এখানে ছাত্রসংখ্যা ছিল দশ হাজার এবং বৌদ্ধগণের আঠারোটি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন। ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যতীত বেদ, হেতুবিদ্যা, শব্দবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, ও সাংখ্য, প্রভৃতি এখানে অধীত হইত। হুয়েন সাং বলেন যে, এক শীলভদ্রই একা এই সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং সংঘবাসীগণ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবশত তাঁহার নাম উচ্চারণ না করিয়া তাহাকে ‘ধর্ম্মনিধি’ বলিয়া অভিহিত করিতেন। হুয়েন সাং চীনদেশ হইতে আসিয়াছেন শুনিয়া, শীলভদ্র তাঁহাকে সাদরে শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন এবং যোগশাস্ত্র শিক্ষা দেন। আ ৬৫৪ অব্দে শীলভদ্রের মৃত্যু হয়।
শীলভদ্র ব্যতীত আরও দুইজন বাঙ্গালী-শান্তিরক্ষিত ও চন্দ্রগোমিন-নালন্দার আচাৰ্যপদ লাভ করিয়াছিলেন। শান্তিরক্ষিতের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। চন্দ্রগোমিন বরেন্দ্রে এক ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাহিত্য, ব্যাকরণ, ন্যায়, জ্যোতিষ, আয়ুর্ব্বেদ, সঙ্গীত ও অন্যান্য শিল্পকলায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন এবং আচাৰ্য অশোকের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা লাভ করেন। তিনি প্রথমে দাক্ষিণাত্য ও সিংহল-দ্বীপে বাস করেন এবং চান্দ্র-ব্যাকরণ নামে একখানি ব্যাকরণগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি নালন্দায় গমন করিলে, প্রথমে তথাকার আচাৰ্য্যগণ তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু নালন্দার প্রধান আচাৰ্য্য চন্দ্রকীৰ্ত্তি তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন। তিনি নালন্দায় একটি শোভাযাত্রার ব্যবস্থা করেন। ইহার সম্মুখভাগে তিনখানি রথ ছিল। ইহার একখানিতে চন্দ্রগোমিন আর একখানিতে মঞ্জুশ্রীর মূর্ত্তি, এবং তৃতীয়খানিতে স্বয়ং চন্দ্রকীর্তি ছিলেন। ইহার পর হইতে নালন্দায় চন্দ্রগোমিনের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায় এবং যোগাচার-মতবাদ সম্বন্ধে বিচার-বিতর্ক করিয়া তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।
নালন্দার ন্যায় বিক্রমশীল বিহারেও অনেক বাঙ্গালী আচাৰ্য্য ছিলেন। দীপঙ্করের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অভয়াকরগুপ্ত এই মহাবিহারের সর্বাধ্যক্ষের পদ লাভ করিয়াছিলেন এবং তিনি এখনো তিব্বতে একজন পঞ্ছেন-রিণপোছে অর্থাৎ রাজগুণালঙ্কৃত লামারূপে পূজিত হন। গৌড় নগরীর নিকটে তাঁহার জন্ম হয় এবং তিনি বৌদ্ধ পণ্ডিতরূপে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি প্রথমে রামপালের রাজপ্রাসাদে বৌদ্ধ আচাৰ্য নিযুক্ত হন এবং ওদন্তপুরী বিহারের মহাযান সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব লাভ করেন। কালক্রমে তিনি বিক্রমশীল মহাবিহারের প্রধান আচার্য পদে নিযুক্ত হন। ঐ বিহারে তখন তিন হাজার ভিক্ষু বাস করিতেন। তিনি তিব্বতে গিয়াছিলেন কি না সঠিক বলা যায় না, কিন্তু বহু গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিরেন। রামপালের রাজ্যাবসানের পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। তিনি দিবসের প্রথম দুইভাগে শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা করিতেন, তৃতীয় ভাগে ধৰ্ম্মব্যাখ্যা করিতেন এবং তারপর দ্বিপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত হিমবন শ্মশানে দেবার্চনা করিয়া শয়ন করিতেন। সুখবতী নগরীর বহু ক্ষুধিত ভিক্ষুককে তিনি অন্নদান করেন। চরসিংহ নগরের এক চণ্ডাল রাজা একশত নরবলী দিবার সংকল্প করেন, কিন্তু তাঁহার অনুরোধে প্রতিনিবৃত্ত হন। একবার একদল ‘তুরুষ্ক’ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে তিনি কয়েকটি ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন এবং তাঁহার ফলে তুরুষ্কেরা ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হয়। অবশ্য এই গল্পগুলি কত দূর সত্য বলা কঠিন।
তিব্বতীয় লামা তারনাথ জেরি নামক আর একজন বাঙ্গালী আচার্যের কিছু বিবরণ দিয়াছেন। জেরির পিতা ব্রাহ্মণ আচাৰ্য্য গর্ভপাদ বরেন্দ্রের রাজা সনাতনের গুরু ছিলেন। বরেন্দ্রেই জেতারির জন্ম হয়। অল্প বয়সেই জ্ঞাতিগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া জেরি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং বৌদ্ধশাস্ত্রে, বিশেষত অভিধর্ম্মপিটকে, বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। রাজা মহাপাল (মহীপাল?) তাহাকে বিক্রমশীল বিহারের পণ্ডিত-এই গৌরবময় পদসূচক একখানি মানপত্র দান করেন। তিনি বহুদিন এই বিহারের আচাৰ্য্য ছিলেন এবং তাঁহার দুই ছাত্র রত্নাকরশান্তি ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান পরে এই মহাবিহারের সাধ্যক্ষ পদ লাভ করিয়াছিলেন। তারনাথের মতে তিনি একশত গ্রন্থ রচনা করেন। ইহার অনেকগুলিই তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল।
দীপঙ্করের আর একজন অধ্যাপক জ্ঞানশ্রীও বাঙ্গালী ছিলেন। তিনি বিক্রমশীল মহাবিহারের দ্বারপণ্ডিত ছিলেন। কাশ্মীরে জ্ঞানশ্রীদ্র নামে এক বৌদ্ধ আচার্য্যের খ্যাতি আছে, তিনি ও এই জ্ঞানশ্রী সম্ভবত একই ব্যক্তি। তিনি বহু গ্রন্থ লিখিয়াছেন এবং তিব্বতীয় ভাষায় ইহার অনেকগুলির অনুবাদ হইয়াছিল।
বৌদ্ধ আচাৰ্য ব্যতীত বাংলার অনেক শৈব গুরুও বাংলার বাহিরে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। দক্ষিণরাঢ়া নিবাসী উমাপতিদেব (অপর নাম জ্ঞানশিব দেব) চোলদেশে বসবাস করেন এবং স্বামিদেবর এই নামে পরিচিত হইয়া রাজা-প্রজা উভয়েরই শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন হন। এই সময়ে চোলরাজ দ্বিতীয় রাজাধিরাজের (১১৬৩-১১৯০) একজন সামন্তরাজা সিংহলদেশীয় সৈন্যের আক্রমণে ভীত হইয়া উমাপতিদেবের শরণাপন্ন হন। উমাপতিদেব ২৮ দিন শিবের আরাধনা করেন এবং তাঁহার ফলে সিংহলীয় সৈন্য চোলরাজ্য ত্যাগ করিয়া পলাইয়া যায়। কৃতজ্ঞ সামন্তরাজা উমাপতিদেবকে একখানি গ্রাম দান করেন এবং উমাপতি ইহার রাজস্ব তাঁহার আত্মীয়দের মধ্যে ভাগ করিয়া দেন।
জব্বলপুরের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন ডাহলমণ্ডলে গোলকীমঠ নামে এক বিখ্যাতি শৈব প্রতিষ্ঠান ছিল। কলচুরিরাজ প্রথম যুবরাজ (আ ৯২৫ অব্দ) এই মঠের অধ্যক্ষকে তিন লক্ষ গ্রাম দান করেন। ইহার আয় হইতে মঠের ব্যয় নির্বাহ হইত। বাঙ্গালী বিশ্বেশ্বরশম্ভু ত্রয়োদশ শতাব্দের মধ্যভাগে এই মঠের অধ্যক্ষপদ লাভ করেন। দক্ষিণ রাঢ়ার অন্তর্গত পূৰ্ব্বগ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। বেদে অগাধ পাণ্ডিত্যহেতু তিনি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। চোল ও মালবরাজ তাঁহার শিষ্য ছিলেন এবং কাকতীয়রাজ গণপতি ও ত্রিপুরীর কলচুরিরাজ তাঁহার নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি মন্ত্রশিষ্য রাজা গণপতির রাজ্যে বাস করিতেন। গণপতি এবং তাঁহার কন্যা ও উত্তরাধিকারিণী রুদ্রাম্বা তাঁহাকে দুইখানি গ্রাম দান করেন। বিশ্বেশ্বরশম্ভু এই দুইখানি গ্রাম একত্র করিয়া বিশ্বেশ্বর-গোলকী নামে অভিহিত করেন এবং তথায় মন্দির, মঠ, বিদ্যালয়, অন্নছত্র, মাতৃশালা ও আরোগ্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই গ্রামে ৬০টি দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ-পরিবার বসতি করান এবং তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য উপযুক্ত ভূমিদান করেন। অবশিষ্ট ভূমি তিনভাগে বিভক্ত করা হয়। একভাগ শিবমন্দির, আর একভাগ বিদ্যালয় ও শৈবমঠ, এবং তৃতীয় ভাগ অবশিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয়-নির্বাহের জন্য নির্দিষ্ট হয়। বিদ্যালয়ের জন্য আটজন অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনজন ঋক, যজু ও সাম এই তিন বেদ পড়াইতেন, আর বাকি পাঁচজন সাহিত্য, ন্যায় ও আগম শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলির জন্যও যথোচিত কর্ম্মচারী ও সেবক প্রভৃতি নিযুক্ত হয়। গ্রামের লোকের জন্য একঘর করিয়া স্বর্ণকার, কৰ্ম্মকার, শিলাকার, সূত্রধর, কুম্ভকার, স্থপতি, নাপিত প্রভৃতি স্থাপিত করা হয়। বিশ্বেশ্বরশঙ্কু জন্মভূতি পূৰ্ব্বগ্রাম হইতে কয়েকজন ব্রাহ্মণ আনাইয়া গ্রামের আয়-ব্যয় পরীক্ষা ও হিসাবরক্ষকের কাৰ্য্যে নিযুক্ত করেন। গ্রামের বিবিধ প্রতিষ্ঠানগুলি যাহাতে ভবিষ্যতে উপযুক্তরূপে পরিচালিত হয়, তাঁহার জন্য তিনি অনেক বিধিব্যবস্থা করেন। বিশ্বেশ্বরশম্ভু আরও বহু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন এবং বিভিন্ন স্থানে মঠ, মন্দির ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার ব্যয় নির্বাহের জন্য উপযুক্ত জমি দান করেন। বিশ্বেশ্বর নামে তিনি একটি নগরী স্থাপন করেন। শিলালিপিতে এই সমুদয়ের যে সবিস্তার উল্লেখ আছে, তাহা পাঠ করিলে প্রাচীন যুগের বাঙ্গালীর জীবনযাত্রা, সমাজের প্রতি কর্তব্য এবং ধর্ম্মসংস্কার প্রভৃতির আদর্শ আমাদের নিকট উজ্জ্বল হইয়া ওঠে।
বাঙ্গালী বৎস-ভার্গব গোত্রীয় ব্রাহ্মণ বসাবণ হরিয়াণ (পঞ্জাবের হিসার জিলার অন্তর্গত হরিয়ান) প্রদেশের সিংহপল্লী গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ঈশানশিব সংসার ত্যাগ করিয়া বোদামযুতের (যুক্ত প্রদেশের বাউন) শৈব-মঠে বাস করেন। কালক্রমে তিনি এই মঠের অধ্যক্ষ হন এবং একটি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। গৌড়দেশীয় অবিঘ্নাকর কৃষ্ণগিরি পাহাড়ে (বম্বের অন্ত গত কাহ্নেরি) ভিক্ষুদের বসবাসের জন্য একটি গুহা খনন করান। তিনি ৮৫৩ অব্দে একশত দ্রম্ম দান করেন। এই গচ্ছিত অর্থের সুদ হইতে উক্ত গুহা বিহারবাসী ভিক্ষুগণকে বস্ত্র দিবার ব্যবস্থা করা হয়।
কয়েকজন বাঙ্গালী পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের জন্য বাংলার বাহিরে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। শক্তিস্বামী নামে একজন বাঙ্গালী কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার পুত্র কল্যাণস্বামী যাজ্ঞবন্ধ্যের তুল্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন। কল্যাণস্বামীর পৌত্র জয়ন্ত একজন কবি ও বাগ্মী ছিলেন এবং বেদ-বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। অনেকে মনে করেন যে, তিনি ও ন্যায়মঞ্জরী-প্রণেতা জয়ন্তভট্ট একই ব্যক্তি। এই জয়ন্তের পুত্র অভিনন্দন কাদম্বরী-কথাসার গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে বাণভট্ট-প্রণীত কাদম্বরীর সারমর্ম কবিতায় বর্ণিত হইয়াছে। ভট্টকোশল-গ্রাম-নিবাসী বাঙ্গালী লক্ষ্মীধর একজন সুপরিচিত কবি ছিলেন। তিনি মালবে গমন করেন এবং পরমাররাজ ভোজের (১০০০-১০৪৫) সভা অলঙ্কৃত করেন। তিনি চক্রপাণি-বিজয় নামক একখানি কাব্য প্রণয়ন করেন। দক্ষিণ রাঢ়ার অন্তর্গত নবগ্রাম-নিবাসী হলায়ূধও মালবে বাসস্থাপন করেন। তাঁহার রচিত ৬৪টি শ্লোক মান্ধাতা (প্রাচীন মাহিম্মতী?) নগরের এক মন্দিরগাত্রে উত্তীর্ণ হয় (১০৬৩ অব্দ)। মদন নামে আর একজন বিখ্যাত বাঙ্গালী কবি বাল্যকালে মালবে গিয়া তাঁহার কবিত্বশক্তির জন্য বাল-সরস্বতী উপাধি প্রাপ্ত হন এবং পরমাররাজ অর্জুন বর্ম্মার (১২১০-১২১৮) গুরুপদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি পারিজাতমঞ্জরী’ নামক কাব্য রচনা করেন। চন্দ্রেরাজ পরমর্দির সভায় বাঙ্গালী গদাধর ও তাঁহার দুই পুত্র দেবর ও ধৰ্মধর এই তিন কবি বাস করিতেন। রামচন্দ্ৰ কবিভারতী নামে আর একজন বাঙ্গালী সুদূর সিংহলদ্বীপে প্রতিপত্তি লাভ করেন। বীরবতী গ্রামে তাঁহার জন্ম হয় এবং অল্পবয়সেই তিনি তর্ক, ব্যাকরণ, শ্রুতি, স্মৃতি, মহাকাব্য, আগম, অলঙ্কার, ছন্দ, জ্যোতিষ ও নাটক প্রভৃতিতে পারদর্শী হন। রাজা দ্বিতীয় পরাক্রমবাহুর রাজ্যকালে (১২২৫-৬০) তিনি সিংহলে গমন করিয়া বৌদ্ধ আচার্য্য রাহুলের শিষ্যত্ব গ্রহণ ও বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা লাভ করেন। রাজা পরাক্রমবাহু তাহাকে ‘বৌদ্ধগমচক্রবর্ত্তী এই সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করেন। রামচন্দ্র ভক্তিশতক, বৃত্তমালা ও বৃত্তরত্নাকর-পঞ্জিকা এই তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থের রচনাকাল ১২৪৫ অব্দ।
গৌড়দেশীয় করণ-কায়স্থগণ সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান ও লিপি-কুশলতার জন্য আৰ্য্যাবর্তের সর্বত্র বিখ্যাত ছিলেন ও প্রাচীন লিপি উৎকীর্ণ করিবার জন্য নিযুক্ত হইতেন। চন্দ্রে, চাহমন ও কলচুরি রাজগণের অনেক লিপি হঁহাদের দ্বারা উৎকীর্ণ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন বিহার ও যুক্তপ্রদেশের কয়েকখানি লিপির লেখকও বাঙ্গালী ছিলেন।
এতক্ষণ আমরা কেবল ধর্ম্মাচাৰ্য, কবি ও পণ্ডিত সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্যেও অনেক বাঙ্গালী বাংলার বাহিরে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। গদাধর বরেন্দ্রের অন্তর্গত তড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণ (৯৩৯-৯৬৮) ও খোট্টিগের অধীনে কার্তিকেয়-তপোবন নামক ভূখণ্ডের অধিপতি হন। মাদ্রাজ-প্রদেশের অন্তর্গত বেলারী জিলার কোলগলুগ্রামে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি এই স্থানে একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্ৰহ্ম, বিষ্ণু, শিব, পাৰ্ব্বতী, কার্তিক, গণেশ ও সূৰ্য্য প্রভৃতি দেব-দেবীর মূর্ত্তি স্থাপন এবং কুপ-তড়াগাদি খনন করেন। একখানি প্রস্তরলিপিতে তিনি গৌড় চূড়ামণি, বরেন্দ্রীর দ্যোতকারী এবং মুনি ও দুর্ভিক্ষমল্ল (দুর্ভিক্ষের দমনকারী) বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ১১৯১ অব্দে উত্তীর্ণ একখানি লিপিতে গৌড়বংশীয় রাজা অনেকমল্লের উল্লেখ আছে। তিনি গাঢ়ওয়াল অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন এবং কেদারভূমি ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ জয় করেন। সপ্তম শতাব্দীতে শক্তি নামক ভরদ্বাজ-বংশীয় একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ দৰ্বাভিসারের অধিপতি হন। এই স্থান পঞ্জাবের চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা নদীর মধ্যস্থলে পার্ব্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত। তাঁহার পৌত্র শক্তিস্বামী কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড়ের মন্ত্রী হইয়াছিলেন। বাঙ্গালী লক্ষ্মীধরের পুত্র গদাধর চন্দেল্লরাজগণের মরমর্দির (১১৬৭-১২০২) সান্ধিবিগ্ৰহিক পদ লাভ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মীধর নামে আর একজন বাঙ্গালী ও তাঁহার বংশধরগণ সাত পুরুষ যাবৎ চন্দেল্লরাজগণের অধীনে কর্ম্ম করেন। ইহার মধ্যে তিনজন-যশঃপাল, গোকুল ও জগদ্ধর-রাজমন্ত্রীর পদ লাভ করিয়াছিলেন। দেড়শত বৎসরের অধিককাল (আ ১১০০-১২৫০) এই বাঙ্গালী পরিবার চন্দেল্লরাজ্যে উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত থাকিয়া। বাঙ্গালীর শাসনকার্যে দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। পঞ্চম শতাব্দের একখানি লিপি হইতে জানা যায় যে, ‘গৌরী’ দেশের এক ক্ষত্রিয় রাজপুতানার উদয়পুরে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। এই গৌর সম্ভবত গৌড় দেশ এবং এই রাজপরিবার সম্ভবত বাঙ্গালী ছিলেন।
চাহমানরাজ তৃতীয় পৃথ্বীরাজের নাম ইতিহাসে সুপরিচিত। মুহম্মদ ঘোরীকে প্রথম যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পরে দ্বিতীয় যুদ্ধে কিরূপে তিনি পরাজিত ও নিহত হন, মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু হম্মীর মহাকাব্যে এই যুদ্ধের অন্য রকম বিবরণ পাওয়া যায় এবং এই প্রসঙ্গে উদয়রাজ নামক একজন বাঙ্গালী বীরের কীর্তি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। উদয়রাজ পৃথ্বীরাজের সেনাপতি ছিলেন। পৃথ্বীরাজ ঘোরীর সহিত বহু যুদ্ধে জয়লাভ করেন। কিন্তু একবার ঘোরী পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণ করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। পৃথ্বীরাজ উদয়রাজকে সসৈন্যে অগ্রসর হইতে আদেশ করিয়া নিজে অল্প সৈন্য লইয়া শত্রুর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং পরাজিত ও বন্দী হন। উদয়রাজ সসৈন্যে উপস্থিত হইলে, ঘোরী তাঁহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া বন্দী পৃথ্বীরাজসহ দিল্লীর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। গৌড়বীর প্রভুর পরাজয়েও হতাশ না হইয়া দিল্লী আক্রমণ করেন এবং এক মাসকাল যুদ্ধ করেন। ঘোরীর অমাত্যগণ উদয়রাজের পরাক্রমে ভীত হইয়া শান্তি স্থাপনের নিমিত্ত পৃথ্বীরাজকে মুক্তি দিবার পরামর্শ দিলেন। ঘোরী তাহা না শুনিয়া পৃথ্বীরাজকে বধ করিলেন। প্রভুর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া উদয়রাজ দিল্লী অধিকার করিবার জন্য প্রাণপণে শেষ চেষ্টা করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। হম্মীর-মহাকাব্যের এই কাহিনী কত দূর বিশ্বাসযোগ্য বলা কঠিন, কিন্তু উদয়রাজের বীরত্বকাহিনী একেবারে নিছক কল্পনা, এরূপ অনুমান করাও সঙ্গত নহে। হিন্দু যুগের অবসানে একজন গৌড়ীয় বীর সুদূর পশ্চিমে তুরষ্কসেনার সহিত সংগ্রামে আত্মবিসৰ্জন করিয়া প্রভুভক্তির চরম প্রমাণ দিয়াছিল, বিদেশীয় কবির এই কল্পনাও বাঙ্গালীর পক্ষে কম শ্লাঘার বিষয় নহে।
বাংলার বাহিরে বাঙ্গালী কিরূপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিল, তাঁহার যে কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছি, তাহাই লিপিবদ্ধ হইল। কালসমুদ্রে এইরূপ আর কত বিষ্মকর কাহিনী ও কীর্তিগাথা বিলীন হইয়াছে কে বলিতে পারে? পঞ্জাবের পার্ব্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত সুকেত, কেওস্থল, কাষ্টওয়ার ও মণ্ডী এই কয়টি রাজ্যের রাজগণ বাংলার গৌড়-রাজবংশ-সদ্ভূত, এইরূপ একটি বদ্ধমূল সংস্কার দীর্ঘকাল যাবৎ ঐ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। কাষ্টওয়ার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কাহনপাল সম্বন্ধে প্রচলিত জনশ্রুতি এই যে, তিনি গৌড়ের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং কতিপয় অনুচরসহ উক্ত পার্ব্বত্য অঞ্চলে গমন করিয়া একটি রাজ্য স্থাপন করেন। পালবংশীয় সম্রাটগণ এই প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, এবং পরবর্ত্তীকালে তাঁদের অথবা সেনরাজগণের বংশের কেহ এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিতে পারেন। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত জনশ্রুতি একেবারে অমূলক বা অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তবে বিশ্বস্ত প্রমাণ না পাইলে, ইহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়াও গ্রহণ করা যায় না।
২২. বাংলার ইতিহাস ও বাঙ্গালীজাতি
দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ – বাংলার ইতিহাস ও বাঙ্গালীজাতি
প্রকৃত ইতিহাস বলিতে আমরা যাহা বুঝি, প্রাচীন বাংলার সেরূপ ইতিহাস লেখার সময় এখনো আসে নাই। কখনো আসিবে কি না তাহাও বলা যায় না। আমাদের দেশে এই যুগে লিখিত কোনো ঐতিহাসিক গ্রন্থ নাই। সুতরাং বিদেশীয় লেখকের বিবরণ এবং প্রাচীন লিপি, মুদ্রা ও অতীতের অন্যান্য স্মৃতিচিহ্নই এই ইতিহাস রচনার প্রধান উপকরণ। এ পর্য্যন্ত যে সমুদয় উপকরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাঁহার সাহায্যে যত দূর সম্ভব পুরাতন ঐতিহাসিক কাহিনী বিবৃত করিয়াছি। কিন্তু ইহা বাংলার ইতিহাস নহে, তাঁহার কঙ্কালমাত্র। ভূগর্ভে নিহিত অন্যান্য প্রাচীন লিপি, মুদ্রা প্রভৃতি অথবা রামচরিতের ন্যায় গ্রন্থ বহু সংখ্যায় আবিষ্কৃত হইলে হয়ত এই ইতিহাসের কঙ্কালে রক্তমাংসের যোজনা করিয়া ইহাকে সুগঠিত আকার প্রদান করা সম্ভবপর হইবে। কিন্তু তাহা কত দিনে হইবে, অথবা কখনো হইবে কি না, তাহা কেহ বলিতে পারে না।
আজ বাংলার ইতিহাসের উপকরণ পরিমাণে মুষ্টিমেয়। কিন্তু মুষ্টি হইলেও ইহা ধূলিমুষ্টি নহে, স্বর্ণমুষ্টি। ইহার সাহায্যে আমরা বাঙ্গালীর রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধৰ্ম্মজীবনের প্রকৃতি, গতি ও ক্রমবিবর্ত্তন জানিতে পারি না, এমনকি তাঁহার সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণাও করিতে পারি না, একথা সত্য। কিন্তু তথাপি এই সমুদয় সম্বন্ধে যে ক্ষীণ আভাস বা ইঙ্গিত পাই, তাঁহার মূল্য খুবই বেশি। আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা যে কত গভীর ছিল, এবং গত একশত বৎসরে এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান কত দূর অগ্রসর হইয়াছে, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত রাজাবলী গ্রন্থের সহিত এই ইতিহাসের তুলনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কতকগুলি নিছক গল্প ও অলীক কাহিনীই ইতিহাস নামে প্রচলিত ছিল। বাঙ্গালীর অতীত কীর্তি বিস্মৃতির নিবিড় অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছিল।
আজ ইতিহাসের একটু টুকরামাত্র আমরা জানি। কিন্তু হীরার টুকরার মতোই ইহার ভাস্করদীপ্তি অতীতের অন্ধকার উজ্জ্বল করিয়াছে। বিজয়সিংহের কাল্পনিক সিংহল-বিজয়কাহিনীই বাঙ্গালীর সাহস ও বীরত্বের একমাত্র নিদর্শন বলিয়া এত দিন গণ্য ছিল। আজ আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, বাঙ্গালীর বাহুবল সত্য-সত্যই একদিন তাঁহার গর্বের বিষয় ছিল। বাঙ্গালী শশাঙ্ক কান্যকুব্জ হইতে কলিঙ্গ পৰ্য্যন্ত বিজয়াভিযান করিয়া যে সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী ধর্ম্মপাল ও দেবপাল তাঁহার পরিকল্পনা সম্পূর্ণ করিয়া সূদূর পঞ্চনদ অবধি বাহুবলে বাঙ্গালীর রাজশক্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী ধর্ম্মপাল কান্যকুজের রাজসভায় সম্রাটের আসনে বসিতেন, আর সমগ্র আর্য্যাবর্তের রাজন্যবৃন্দ প্রণত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিতেন। গঙ্গাতীরে মৌৰ্য্যসম্রাট অশোকের কীর্তিপূত পাটলিপুত্র নগরীর রাজসভায় ভারতের দূর-দূরান্তর প্রদেশ হইতে আগত সামন্ত রাজন্যবর্গ বহুমূল্য উপঢৌকনসহ নতশিরে দণ্ডায়মান হইয়া পালসম্রাটের প্রতীক্ষা করিতেন। ইহা স্বপ্ন নহে, সত্য ঘটনা। আজ বাঙ্গালী ভীরু দুব্বল বলিয়া খ্যাত, ভারতের সামরিক শক্তিশালী জাতির পংক্তি হইতে বহিষ্কৃত-কিন্তু আমাদের অতীত ইতিহাস মুক্তকণ্ঠে ইহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে।
মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতেও বাঙ্গালী বলীয়ান ছিল। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বিতাড়িত বৌদ্ধধর্ম্ম বাঙ্গালীর রাজ্যই শেষ আশ্রয় লাভ করিয়া চারিশত বৎসর টিকিয়াছিল। এই সুদীর্ঘকাল বাঙ্গালী বৌদ্ধজগতের গুরুস্থানীয় ছিল। উত্তরে দুর্গম হিমগিরি পার হইয়া তিব্বতে তাহারা ধর্ম্মের নতুন আলো বিকীর্ণ করিয়াছিল। দক্ষিণে দুর্লঙ্ জলধির পরপারে সুদূর সুবর্ণদ্বীপ পর্য্যন্ত বাঙ্গালী রাজার দীক্ষা গুরুপদে অভিষিক্ত হইয়াছিল। জগদ্বিখ্যাত নালন্দা ও বিক্রমশীল বিহার, বাংলার বাহিরে অবস্থিত হইলেও, চারিশত বৎসর পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর রাজশক্তি, মনীষা ও ধর্ম্মভাবের দ্বারাই পরিপুষ্ট হইয়াছিল।
বাণিজ্য-সম্পদে একদিন বাঙ্গালী ঐশ্বৰ্য্যশালী ছিল। তাম্রলিপ্তি হইতে তাঁহার বাণিজ্যপোত সমুদ্র পার হইয়া দূর-দূরান্তরে যাইত। বাংলার সূক্ষ্ম বস্ত্রশিল্প সমুদয় জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।
সংস্কৃত-সাহিত্যেও বাঙ্গালীর দান অকিঞ্চিৎকর নহে। জয়দেবের কোমল কান্ত পদাবলী সংস্কৃত-সাহিত্যের বুকে কৌস্তুভ-মণির ন্যায় চিরকাল বিরাজ করিবে। যত দিন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা থাকিবে তত দিন, গৌড়ী রীতি এবং বল্লালসেন, হলায়ূধ, ভবদেবভট্ট, সর্ব্বানন্দ, চন্দ্রগোমিন, গৌড়পাদ, শ্রীধরভট্ট, চক্রপাণিদত্ত, জীমূতবাহন, অভিনন্দন, সন্ধ্যাকরনন্দী, ধোয়ী, গোবর্দ্ধনাচাৰ্য্য ও উমাপতিধর প্রভৃতির রচনা সমগ্র ভারতে আদৃত হইবে। বাংলার সিদ্ধাচার্যগণের মূল গ্রন্থগুলি যদি কখনো আবিষ্কৃত হয়, তবে বাঙ্গালীর প্রতিভার নূতন এক দিক উদ্ভাসিত হইবে।
শিল্পজগতে মধ্যযুগে বাঙ্গালীর স্থান অতিশয় উচ্চে। ভারতের প্রাচীন শিল্পকলা যখন ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছিল, যখন লাবণ্য ও সুষমার পরিবর্তে প্রাণহীন ধৰ্ম্মভাবের ব্যঞ্জনাই শিল্পের আদর্শ হইয়া উঠিয়াছিল, তখন বাঙ্গালী শিল্পীই মূৰ্ত্তিগঠনে ও চিত্রকলায় প্রাচীন চারুশিল্পের কমনীয়তা ও সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সোমপুরে বাঙ্গালী যে বিহার ও মন্দির নির্মাণ করিয়াছিল, সমগ্র ভারতে তাঁহার তুলনা মিলে না। বাংলার স্থপতিশিল্প ও ভাস্কৰ্য্য সমগ্র পূর্ধ্ব এশিয়ায় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।
এইরূপে যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, প্রাচীন যুগের বাঙ্গালীর কীৰ্ত্তি ও মহিমা আমাদের নয়ন-সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। আমাদের ধারাবাহিক ইতিহাস না থাকিলেও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি বিবরণ হইতে সেকালের যে পরিচয় পাওয়া যায়, বাঙ্গালীমাত্রেরই তাহাতে গৌরব বোধ করার যথেষ্ট কারণ আছে। এই স্বল্প পরিচয়টুকু দিবার জন্যই এই গ্রন্থের আয়োজন। হয়ত ইহার ফলে বাঙ্গালীর মনে অতীত ইতিহাস জানিবার প্রবৃত্তি জন্মিবে এবং সমবেত চেষ্টার ফলে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা সম্ভবপর হইবে।
আমরা এই গ্রন্থে বাঙ্গালী এই সাধারণ সংজ্ঞা ব্যবহার করিয়াছি। কিন্তু যে যুগের কাহিনী এই ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সে যুগের বাঙ্গালী আর আজিকার বাঙ্গালী ঠিক একই অর্থ সূচিত করে না। যে ভূখণ্ড আজ বঙ্গদেশ বলিয়া পরিচিত, প্রাচীন যুগে তাঁহার বিশিষ্ট কোনো একটি নাম ছিল না এবং তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইত, একথা গ্রন্থারম্ভেই বলিয়াছি। আজ যে ছয় কোটি বাঙ্গালী একটি বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত হইয়াছে, ইহার মূলে আছে ভাষার ঐক্য এবং দীর্ঘকাল একই দেশে এক শাসনাধীনে বসবাস। ধর্ম্ম ও সমাজগত গুরুতর প্রভেদ সত্ত্বেও এই দুই কারণে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসী হইতে পৃথক হইয়া বাঙ্গালী একটি বিশিষ্ট জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যে প্রাচীন যুগের কথা আমরা আলোচনা করিয়াছি, সে যুগের বাংলায় এমন একটি স্বতন্ত্র বিশিষ্ট প্রাদেশিক ভাষা গড়িয়া ওঠে নাই, যাহা সাহিত্যের বাহনরূপে গণ্য হইতে পারে সুতরাং তখন সারা বাংলার প্রচলিত ভাষা মোটামুটি এক এবং অন্যান্য প্রদেশের ভাষা হইতে পৃথক হইলেও তাহা জাতীয়তা গঠনের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল, এইরূপ মনে হয় না। সমগ্র বাংলা পাল ও সেনরাজগণের রাজ্যকালে তিন-চারিশত বৎসর যাবৎ মোটামুটি একই শাসনের অধীনে থাকিলেও কখনো এক দেশ বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। হিন্দু যুগের শেষ পর্য্যন্ত গৌড় ও বঙ্গ দুইটি পৃথক দেশ সূচিত করিত। ইহার প্রত্যেকটিরই সীমা ক্রমশ ব্যাপক হইতে হইতে সমগ্র বাংলা দেশ তাঁহার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল-কিন্তু হিন্দু যুগের অবসানের পূর্ব্বে তাহা হয় নাই। তখন পর্য্যন্ত সমগ্র বাংলা দেশের কোনো একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা গড়িয়া ওঠে নাই। কঠোর জাতিভেদ প্রথা তখন ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জাতির মধ্যে একটি সুদৃঢ় ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছিল, এবং বাংলার ব্রাহ্মণ সম্ভবত বাংলার অন্য জাতির অপেক্ষা ভারতের অন্যান্য প্রদেশস্থ ব্রাহ্মণের সহিত অধিকতর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ ছিল। এই সমুদয় কারণে মনে হয় যে, হিন্দু যুগে বাঙ্গালী অর্থাৎ সমগ্র বাংলা দেশের অধিবাসী একটি বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত হয় নাই।
কিন্তু তখন গৌড়বঙ্গের অধিবাসীরা যে দ্রুতগতিতে এক জাতিতে পরিণত হইবার দিকে অগ্রসর হইতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। দীর্ঘকাল এক রাজ্যের অধীনে এবং পরস্পরের পাশাপাশি বাস করিবার ফলে, তাহাদের সম্বন্ধ ক্রমশই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল এবং তাহারা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে পৃথক হইয়া কতকগুলি বিষয়ে বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র অবলম্বন করিতেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহাদের মৎস্য-মাংস-ভোজন, কোনো প্রকার শিরোভূষণের অব্যবহার, তান্ত্রিক মত ও শক্তিপূজার প্রাধান্য, প্রাচীন বঙ্গভাষা ও লিপির উৎপত্তি এবং শিল্পের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এ সমুদয়ই তাহাদিগকে নিকটবর্ত্তী অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসী হইতে পৃথক করিয়া একটি বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছিল। এই বৈশিষ্ট্যের ফলেই, হিন্দু যুগের অবসানের অনতিকাল পরেই, তাহারা একটি জাতিতে পরিণত হইয়াছিল এবং ক্রমে তাহাদের এক নাম ও সংজ্ঞার সৃষ্টি হইয়াছিল। বিদেশীয় তুরস্করাজগণ তাহাদের এই জাতীয় বৈশিষ্ট লক্ষ্য করিয়া তাহাদিগকে একই নামে অভিহিত করেন। ইহারই ফলে গৌড় ও বঙ্গালদেশ মুসলমান যুগে সমগ্র বাংলা দেশের নামস্বরূপ ব্যবহৃত হয় এবং গৌড়ীয়’ ও ‘বাঙ্গালী’ সমগ্র দেশবাসীর পক্ষে প্রযোজ্য এই দুইটি জাতীয় নামের সৃষ্টি হয়। ইহাই বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।