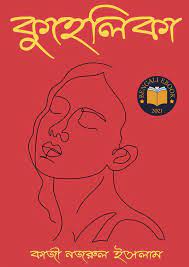- বইয়ের নামঃ কুহেলিকা
- লেখকের নামঃ কাজী নজরুল ইসলাম
- প্রকাশনাঃ স্টুডেন্ট ওয়েজ
- বিভাগসমূহঃ উপন্যাস
কুহেলিকা – ০১
নারী লইয়া আলোচনা চলিতেছিল। …
তরুণ কবি হারুণ তাহার হরিণ-চোখ তুলিয়া কপোত-কূজনের মতো মিষ্টি করিয়া বলিল, ‘নারী কুহেলিকা’।
যেস্থানে আলোচনা চলিতেছিল, তাহা আসলে ‘মেস’ হইলেও, হইয়া দাঁড়াইয়াছে একটি পুরোমাত্রায় আড্ডা।
দুই তিনটি চতুষ্পায়া জুড়িয়া বসিয়া প্রায় বিশ বাইশ জন তরুণ। ইহাদের একজন – লক্ষ্মীছাড়ার মতো চেহারা – একজন ইয়ারের ঊরু উপাধান করিয়া আর একজন ইয়ারের দুই স্কন্ধে দুই পা তুলিয়া দিয়া নির্বিকার চিত্তে সিগারেট ফুঁকিতেছে। এ আলোচনায় কেবল তাহারই কোনো উৎসাহ দেখা যাইতেছিল না। নাম তাহার – বখ্তে-জাহাঙ্গীর কী উহা অপেক্ষাও নসিব বুলন্দ দারাজ গোছের একটা কিছু। কিন্তু অব্যবহারের দরুন তাহা এখন আর কাহারও মনে নাই। তাহাকে সকলে উপেক্ষা বা আদর করিয়া উলঝলুল বলিয়া ডাকে। এ নাম দেওয়ার গৌরবের দাবি লইয়া বহু বাগ্বিতণ্ডা হইয়া গিয়াছে। এখন এই নামই তাহার কায়েম হইয়া গিয়াছে। ‘উলঝলুল’ উর্দু শব্দ, মানে এর – বিশৃঙ্খল, এলোমেলো।
কবি হারুণ যখন নারীকে ‘কুহেলিকা’ আখ্যা দিল, তখন কেহ হাসিল, কেহ টিপ্পনী কাটিল, শুধু উলঝলুল কিছু বলিল না। এক টানে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সিগারেট পুড়াইয়া তাহারই পুঞ্জীভূত ধোঁয়া ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করিয়া শুধু বলিল, ‘হুম!’
আমজাদ ওকালতি পড়ে এবং কবিতা লেখার কসরত করে। সে বলিল, তার চেয়ে বলো না কবি, নারী প্রহেলিকা! বাবা, সাত সমুদ্দুর তেরো নদী সাঁতরিয়েও বিবি গুলে-বকৌলির কিনারা করা যায় না! – বলিয়ায় একবার চারিদিকে ঝটিতি চোখের সার্চলাইট বুলাইয়া লইল। মনে হইল, সকলেই তাহার রসিকতায় রসিয়া উঠিয়াছে। কেবল হারুণ যেন একটু মুচকিয়া হাসিল।
উলঝলুল আবার এক রাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত শব্দ করিল–হুম!
একটু যেন বিদ্রুপের আমেজ! আমজাদ অপ্রতিভ ও ক্ষুণ্ন হইল। কেহ কেহ হাসিলও যেন।
আশরাফ নতুন বিবাহ করিয়াছে, তাহার বধূ ত্রয়োদশী – যৌবনোন্মুখী। কিন্তু এত সাধাসাধি করিয়া এত চিঠি লিখিয়া সে কেবল একটি মাত্র পত্রের উত্তর পাইয়াছে। কিন্তু তাহা ঠিক পত্রোত্তর নয়। তাহাতে শুধু লেখা ছিল দুইটি লাইন – ‘রমণীর মন, সহস্র বর্ষেরই সখা সাধনার ধন!’ বধূ রবীন্দ্রনাথ পড়িতেছে! আশরাফ তাহার বাম হাতের তালুর উপর দক্ষিণ হাতের মুষ্টি সজোরে ঠাসিয়া দিয়া বলিল, ‘নারী অহমিকা!’
উলঝলুল এইবার বেশ জোরেই পূর্বমতো শব্দ করিয়া উঠিল – হুম্ম্। এইবার তারই মধ্যে একটু অভিনয়ের কারুণ্যের আমেজ!
সকলে সমস্বরে হাসিয়া উঠিল। মনে হইল, একসঙ্গে এক ঝাঁকা থালা বরতন পড়িয়া ভাঙিয়া গেল!
আশরাফ লাফাইয়া উলঝলুলের চাঁচর-চুলের গুচ্ছ ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া বলিল, ‘এই শালা, অমন করলি যে?’
এমন ইয়ার্কি ইহাদের মধ্যে প্রায়ই হয়।
উলঝলুল ফিরিয়াও দেখিল না। পূর্বের মতো সচ্চিদানন্দ হইয়া শুইয়া সিগারেট ফুঁকিতে লাগিল।
রায়হান কয়েক বৎসর হইতে কলিকাতায় বসিয়া বসিয়া বি. এ. ফেল করিতেছে। ইহারই মধ্যে তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং বিবাহের অপরিহার্য পরিণাম সন্তান-সন্ততি একটু ঘটা করিয়াই আসিতে শুরু করিয়াছে। রায়হান কিন্তু যত তিক্তবিরক্ত হইয়া উঠিতেছে, ততই মোটা হইতেছে। তবে উদরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পা ও মাথা মোটাইয়া কুলাইয়া উঠিতেছে না। মেসে তাহার আদরের ডাকনাম ‘কুম্ভীর মিয়াঁ’। কুম্ভীর মিয়াঁ কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া যাহা বলিল – তাহাতে মনে হইল, কেহ তাহার কণ্ঠে অনেকগুলা বাঁশের চ্যাঁচারি পুরিয়া দিয়াছে!
হাসির হুল্লোড় পড়িয়া গেল।
উলঝলুল এক লম্ফে স্প্রিং-এর পুতুলের মতো লাফাইয়া উঠিয়া বসিল। তাহার পর কুম্ভীর মিয়াঁর ভুঁড়ির উপর দৃষ্টি রাখিয়া আবার সিগারেট ফুঁকিতে লাগিল।
তরিকের রসিক বলিয়া নামডাক আছে। উলঝলুলের দৃষ্টি লক্ষ করিয়া বলিল, ‘কী হে, ভুঁড়ি কসছ নাকি? কত কালি হবে বলো তো!’
আবার হাসির কোরাস! যেন অনেকগুলো নোড়া শানের উপর দিয়া গড়াইয়া যাইতেছে ও আসিতেছে!
উলঝলুল যেন কিছুই শুনিতেছিল না। সে ঊর্ধ্ব-নয়ন হইয়া হুস করিয়া খানিকটা ধোঁয়া ছাড়িয়া জড়িতকণ্ঠে উচ্চারণ করিল, ‘নারী নায়িকা!’
তাহার বলিবার ভঙ্গি ও ঔদাসীন্যের ভাব দেখিয়া সকলে হাসিয়া উঠিল। কে একজন পিছন হইতে তাহার পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া বলিল, ‘বাহবা, কী তেয়সা!’
ইউসুফ একটু স্থূল ধরনের। বেঁকিয়ে বলা সে বুঝিতও না পছন্দও করিত না। সে উলঝলুলকে এ কথার অর্থ আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলিবার জন্য ধরিয়া বসিল।
অনেকেই তাহার সহিত এই অনুরোধে যোগদান করিল।
উলঝলুল অটল। শুধু আর একবার পূর্বের মতো করিয়া বলিল, ‘নারী নায়িকা!’
সকলে তখন হাল ছাড়িয়া দিয়া হারুণকে ধরিয়া বসিল।…
হারুণ সত্যই কবি। তাহার খ্যাতি ইহারই মধ্যে বেশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। তবে সে খ্যাতি হয়তো হেনা-চাঁপা-বকুল-কেয়ার মতো সুতীব্র দূর-সঞ্চারী নয়। গোলাবের মতো যতটুকু গন্ধ যাইতেছে, অন্তত ততটুকু স্থান মিষ্ট স্নিগ্ধতায় ভরপুর করিয়া তুলিতেছে। সুন্দর ছিপছিপে গড়ন। রং বেশ ফর্সাই। একটু উদাস-উদাস ভাব। যেন সে নিজেকে জানে না, চেনে না। অথবা জানিয়াও অবহেলা করে। রং আর রূপ ছাড়া, পৃথিবীর আর কোনো কিছুতে যেন তার আকাঙ্ক্ষা নাই, কৌতূহল নাই। সবচেয়ে সুন্দর তাহার চোখ। অবশ্য দেখিতেও সে প্রিয়দর্শন। চোখ দুটি যেন কোনো সেকালের মোগল-কুমারীর – বাদশাজাদির। তবে কেমন যেন বিষাদখিন্ন। দৃষ্টি আবেশ মাখা স্বপন-জড়িত। যখন সে কারুর পানে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়, মনে হয় – সে যাহাকে দেখিতেছে দৃষ্টি তাহাকে পারাইয়া গিয়াছে – সে দেখার অতীতকে দেখিতেছে।….
সে এইবার বি.এ. দিবে। তবে পড়ায় তাহার বিশেষ ইচ্ছা নাই। পড়ায় মানে – কলেজের পড়ায়। ‘বাজে বই’ সে যথেষ্ট পড়ে। – অর্থাৎ পৃথিবীর নামজাদা এমন কোনো লেখক বা কবি নাই, যাঁহার সম্বন্ধে সে জানে না।
তবু সে মন দিয়াই পড়িতেছে। সে পিতার জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাহার দিকেই তাহাদের সংসার তাকাইয়া আছে – যেমন করিয়া ভিখারি খঞ্জ তাহার একমাত্র অবলম্বন যষ্টির দিকে তাকাইয়া থাকে।
তাহার পিতা অন্ধ, মাতা উন্মাদরোগগ্রস্তা। বাড়িতে দুইটি অবিবাহিতা বোন এবং একটি ছোটো ভাই। পিতা যে পেনশন পান, তাহাতে ভাতে-ভাত খাইয়া দিন চলে, তার বেশি আর চলে না। ছোটো ভাইটি গ্রামের ইস্কুলে পড়ে। সে-ই সংসার দেখে।
হারুণ টিউশনি করিয়া নিজের খরচ চালায় এবং বাড়িতে ছোটো ভাইটিকে নিজে না খাইয়াও দশটি করিয়া টাকা পাঠায়।
বাড়ি তাহার বীরভূম জেলায়।… যাক, যাহা বলিতেছিলাম –
মেস-বাহিনী পাকড়াও করিয়া বসিল হারুণকে, ‘কবি, বলো তোমার কুহেলিকার অর্থ।’
সে কিছু বলিবার আগেই কেহ বলিল, ‘কবি প্রেমে পড়েছে!’ কেহ বলিল, ‘বাবা! যা-সব হেঁয়ালি কবিতা লেখা হচ্ছে আজকাল!’ কেহ বলিল, ‘চোখ দুটি ক্রমেই যে রকম ঢুলুঢুলু হচ্ছে দিন-কে-দিন, কোথায় শিরাজি টানছ বাবা? আমরা কি সে ভাঁটিখানার সন্ধান পেতে পারিনে?’ ইত্যাদি।
হারুণ তাই বলিয়া মিনমিনে ছেলেও নয়। সে বলিল, ‘অত গোলমাল করলে বলি কী করে বলো? আমার বলা তো তোমরাই বলে নিচ্ছ।’
কুম্ভীর মিয়াঁ হাঁকড়াইয়া উঠিল, ‘এই! সব চোপ। বাস, আর একটি কথা কইছ কী – ভুঁড়ি চাপা! একেবারে ব্যাং-চ্যাপটা!’
হারুণ বলিল, ‘নারী শুধু ইঙ্গিত, সে প্রকাশ নয়। নারীকে আমরা দেখি, বেলাভূমে দাঁড়িয়ে – মহাসিন্ধু দেখার মতো। তীরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের যতটুকু দেখা যায়, আমরা নারীকে দেখি ততটুকু। সমুদ্রের জলে আমরা যতটুকু নামতে পারি, নারীর মাঝেও ডুবি ততটুকুই।… সে সর্বদা রহস্যের পর রহস্য-জাল দিয়ে নিজেকে গোপন করছে – এই তার স্বভাব।…
হারুণ যেন দিশা হারাইল। মনে হইল, সে যেন চকোরের মতো চাঁদের সুধা পান করিয়া উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে! সে যেন পরিস্থানে শুইয়া ফুল ফোটার স্বপন দেখিতেছে।
সে বলিয়া যাইতে লাগিল, ‘কী গভীর রহস্য ওদের চোখে-মুখে। ওরা চাঁদের মতো মায়াবী; তারার মতো সুদূর। ছায়াপথের মতো রহস্য।… শুধু আবছায়া, শুধু গোপন! ওরা যেন পৃথিবী হতে কোটি কোটি মাইল দূরে। গ্রহলোক ওদের চোখে চেয়ে আছে অবাক হয়ে – খুকি যেমন করে সন্ধ্যাতারা দেখে। ওদের হয়তো শুধু দেখা যায়, ধরা যায় না। রাখা যায়, ছোঁয়া যায় না। ওরা যেন চাঁদের শোভা, চোখের জলের বাদলা-রাতে চারপাশের বিষাদ-ঘন মেঘে ইন্দ্রধনুর বৃত্ত রচনা করে। দু-দণ্ডের তরে, তারপর মিলিয়ে যায়। ওরা যেন জলের ঢেউ, ফুলের গন্ধ, পাতার শ্যামলিমা। ওদের অনুভব করো, দেখো, কিন্তু ধরতে যেয়ো না।’
সকলে মুগ্ধবিস্ময়ে শুনিতেছিল। কিন্তু তাহারা শুনিতেছিল, না সুন্দরকে – কবিকে দেখিতেছিল, বলা দুষ্কর। হঠাৎ উলঝলুল হারুণের অসমাপ্ত সুরের সহিত সুর রাখিয়া বলিয়া উঠিল, ‘ঢেউ ধরতে গেলেই জলে ডুববে। গন্ধ ধরতে গেলেই বিঁধবে কাঁটা। শ্যামলিমা ধরতে গেলেই বাজবে শাখা। নারী দেবী, ওকে ছুঁতে নেই, পায়ের নীচে গড় করতে হয়।… কিন্তু কবি, নারী নায়িকা। ও ছাড়া নারীর আর কোনো সংজ্ঞাই নেই।’
অনেকেই না বুঝিয়া হাসিল। কেহ মজা অনুভব করিল, কেহ মানে বুঝিল না।
তরিক তাহার রসিক নাম বজায় রাখিবার জন্য দিগ্বসন পর্যন্ত হইতে রাজি। সে মুখ বিকৃত করিয়া স্বর কাঁপাইয়া বলিয়া উঠিল, ‘ওরে ব্যাটা, তাই তোমার তনু দিনের দিন এমন ক্ষীণ হচ্ছে! তুমি যে নায়ক হয়ে বসে আছ, তা কে জানে! তোমার ডিসপেপসিয়া হয়েছে! যাও, শিগগির এক শিশি ‘কুওতে-মেদা’ কিনে খেয়ে ফেলো!’
হাসির তুফান বহিয়া গেল!
উলঝলুল দৃক্পাতও করিল না। নির্বিকারচিত্তে সিগারেট পোড়াইয়া ধূম্রপুঞ্জের সৃষ্টি করিতে লাগিল।
সে বরাবরই এই রকমের ।
হারুণ এই সব বাজে হুল্লোড়ে যোগদান করিতেছিল না বটে, তবে সে যে এসব উপভোগ করিতেছিল, তাহা তাহার মুখ দেখিয়া বেশ বোঝা যাইতেছিল।
হারুণ সাধারণত একটু কম কথা বলে, কিন্তু দরকার হইলে এত বেশি বলে যে, তাহা প্রায় বক্তৃতা হইয়া উঠে।
হারুণের ওপর সকলেরই বেশ একটা সহজ শ্রদ্ধা ছিল। সে শুধু কবি বলিয়াই নয়, মানুষ বলিয়া। তাহাকে কেহ কখনও তরল হইতে দেখে নাই।
কাজেই হারুণ যখন উলঝলুলকে মৃদু হাসিয়া নারী নায়িকা কেন, জিজ্ঞাসা করিল, উলঝলুল তখন তাহার নির্বিকারত্বের বাঁধুনি একটু শিথিল করিল।
সে বলিল, “আমি জানি, নারী মাত্রই নায়িকা। ওরা প্রত্যেকে প্রতিদিন গল্প আর উপন্যাস সৃজন করে চলেছে।… তবে বড্ড বজ্র আঁটুনি – অবশ্য গেরো ফস্কা। কত “চোখের বালি” কত “ঘরে বাইরে”, কত “গৃহদাহ”, “চরিত্রহীন” সৃষ্টি করছে নারী, তার কটাই বা তোমাদের চোখে পড়ে কবি।… যে কোনো মেয়েকে দুটো দিন ভালো করে দেখো, দেখবে লক্ষ্মী-পক্ষী ইত্যাদি চতুর পুরুষের দেওয়া যত সব বিশেষণ কোনোটাই তাকে মানায় না। তবে, নারী বেচারি সংস্কার আর সমাজের খাতিরে সে যা নয় – তাই হবার জন্যে আমরণ সাধনা করছে। সে যুগ যুগ ধরে চতুর পুরুষের ছাঁচে নিজেকে ঢেলে পুরুষকে খুশি করছে। পুরুষ কিন্তু দিব্যি গায়ে ফুঁ দিয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে এবং নারীকে শিখাচ্ছে দাঁড় ও ছোলা কলার মহিমা। সমানে সমানে বোঝাপড়া হলে নারীকে দেখতে শুধু নায়িকা রূপেই। তোমরা নারীকে দেখ, সে যা হলে ভালো হয় – তাই করে আর আমাদের মতো নিরেট মানুষে দেখে, নারীকে সে যা আছে – তার এক চুলও অতিক্রম না করে। তোমরা যারা নারীকে পূজা কর, আমার এ নির্মমতায় হয়তো ব্যথা পাবে, কিন্তু আমি নারীকে পূজা না করলেও অশ্রদ্ধা করিনে এবং শ্রদ্ধা হয়তো তোমাদের চেয়ে বেশিই করি। কিন্তু তাকে অতিরিক্ত অলংকার পরিয়ে সুন্দর করে – সিঁদুর-কঙ্কণ পরিয়ে কল্যাণী করে নয়। আমি সহজ নারীকে, নিরাভরণাকে করি বন্দনা। রাংতার সাজ পরিয়ে নারীকে দেবী করবার সাধনা আমার নয়। তিন হাত নারীকে বারো হাত শাড়ি পরিয়ে বিপুল করে বাইশ সের লুৎফুন্নিসাকে হিরা জহরত সোনাদানা পরিয়ে এক মনি ভারাক্রান্ত করে – নারীকে প্রসংসা করার চাতুরি আমার নয়! তোমরা হয়তো চটবে, কিন্তু আমি বলি কী, জান? আমি চাই রূপের মোমতাজকে। তাজমহল দিয়ে মোমতাজকে আড়াল করার অবমাননা আমাকে পীড়া দেয়। আমার ক্ষমতা যদি থাকত, ওই বন্দনাগার হতে মোমতাজকে আমি মুক্তি দিতাম। কবরের ভিতর যদি শান্তি থাকে, তবে ‘জাহানারা’ ‘মোমতাজ’ বেচারির চেয়ে অনেক শান্তিতে আছে। জাহানারার কবরের শষ্প-আচ্ছাদনকে মানুষের অহংকার দলিত করেনি, কোনো পাষাণ-দেউল তার বুকে বসে তার বাইরের আকাশ আলোকে আড়াল করে দাঁড়ায়নি!…”
সকলে স্তব্ধ হইয়া শুনিতেছিল এই আধ-পাগলের প্রলাপ। কে একজন বলিয়া উঠিল, ‘পাগলের পাগলামিতেও মাঝে মাঝে মানে থাকে!’ উলঝলুল জোরে-জোরে সিগারেট টানিয়া নিমেষে প্রায় দেড়টা সিগারেট পুড়াইয়া ফেলিল। তাহার পর আবার বলিতে আরম্ভ করিল। –
‘দেখো মানুষ যা নয়, সেই মিথ্যায় অভিষিক্ত করে তাকে খুব শ্রদ্ধা দেখাচ্ছ বলে তোমরা খুব বাহবা নিতে পার, কিন্তু আমার শ্রদ্ধা করার ধারা অন্য রকম। মানুষের – তা তিনি নর হন আর নারীই হন – যা আছে তাই নিয়েই তাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার, সম্মান দেখাবার শক্তি ও সাহস আমার আছে। আমার মত অন্তত অতটুকু তৈরি হয়েছে। – শয়তান সৃষ্টি করা সত্ত্বেও আমি স্রষ্টাকে সম্মান করি। তোমরা শয়তানের নিন্দা করে স্রষ্টার ওপর ‘সেনসার মোসন’ আন, প্রকারান্তরে তাঁর সৃষ্টির দোষ ধরে সমালোচনা কর, আমি তা করিনে – এই যা তফাত। তোমরা নারীকে দেবী বলে এই কথাটাই পাকে-প্রকারে স্মরণ করিয়ে দাও যে, সে আসলে মানবী – দেবী হলেই তাকে মানায় ভালো! নারীকে এ অবমাননা করবার দুর্মতি আমার যেন কোনো দিন না হয়।’
তমিজ এতক্ষণ ধরিয়া কথা কহে নাই। সে অতিমাত্রায় রুচিবাগীশ। এই জন্য সকলে তাহাকে বে-তমিজ বলিয়া খ্যাপাইত। তাহার আদর্শ ছিল রামানন্দ ও তুষ্ণীকুমার বাবু। উলঝলুলকে সে সহিতে পারিত না। সে একেবারে খেপিয়া উঠিয়া বলিল, ‘বাবা পাগলা-গাজি, তুমি থামো! তোমার আর বক্তিমে দিতে হবে না! তোমার মতো বিশ্ব-বখাটে ছেলের আদর্শ নিয়ে জগৎ চলছে না আর চলবেও না!’
উলঝলুল হাসিয়া বলিল, “ভাই বে-তমিজ! চটছ কেন? আমি তো তোমার ‘সাধারণ ব্রাহ্ম মন্দিরে’ বা ‘দেবালয়ে’ গিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিনে। তোমার গুরুর আর তোমাদের মতন আদর্শবাদীর ন্যাকামি আর মিথ্যাচার অসহ্য বলেই তো এত ঘা দিই। শয়তানের ওপর আমার কোনো আক্রোশ নেই, কেননা সে যা – তা সে লুকোয় না, তাকে চিনতে কারুর বেগ পেতে হয় না। কিন্তু ভিতরের কড়া-ক্রান্তি-হিসাবরত স্বার্থপর মুদিওয়ালা বানিয়াকে যখন বাইরের আচার্যের দাড়ি দিয়ে ঢাকতে যাও, তখনই আমি আসি ওই পর-দাড়ির মুখোশ খুলে তার ভিতরের বীভৎস কদর্যতা সকলের সামনে তুলে ধরতে। অবশ্য, তার জন্য আমাকেও অনেকটা নীচে নেমে যেতে হয়। কিন্তু যাক, তোমার রুচিবিকারের ভণ্ডামি আর ন্যাকামি নিয়ে আলোচনা করবার যদি দরকার হয় আর একদিন করব। আমাদের যে আলোচনা চলছিল – তাই চলুক।’
হারুণ বলিল, ‘তুমি কি বলছ, নারীর আর যত রূপ মিথ্যা? সেবিকা, প্রীতিময়ী, স্নেহময়ী – এসব রূপ তার ছলনা? এ মূর্তি সে নিয়েছে তার পুরুষের স্তুতি আর বন্দনার প্রতিদানে – কিংবা তা আরও পাবার লোভে? অথবা তাকে এ সাজে সাজিয়েছে ঈর্ষাতুর পুরুষ? তাকে অবগুন্ঠন পরিয়েছে পুরুষ, মানি – কিন্তু সে তো তাকে সুন্দর করার উদ্দেশ্যেই। নারীকে ঘোমটার আড়াল করে দাঁড় করিয়েই তো তাকে পাবার নেশা বাড়িয়ে দিয়েছে হৃদয়ের। এই আড়ালই কাব্য সৃষ্টি করছে। যক্ষকে চিত্রকূটের আড়াল না দিলে কি মেঘদূত-এর সৃষ্টি হত? সীতাকে রাবণ হরণ না করলে কি রামায়ণ পেতাম? দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ কৌরবেরা করেছিল বলেই মহাভারতের মহাদানে আমাদের পাত্র পূর্ণ হয়ে উঠেছে!’
উলঝলুল পুঞ্জীভূত ধূম্র নাসিকা ও মুখ-গহ্বর দিয়া উদ্গিরণ করিয়া আরও কিছু বলিবার আয়োজন করিতেই চা, গুড়ের সন্দেশ এবং লুচি আসিয়া হাজির হইল।
দেখা গেল, যুবকদের কাছেও নারী অপেক্ষা গুড়ের সন্দেশ অনেক মিষ্টি এবং লুচি ও চা ঢের ঢের প্রিয়। গুড়ের সন্দেশ ও লুচিতে নারী ডুবিয়া গেল। তাহাদের খাইবার ধরন দেখিয়া মনে হইল, যেন বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত অথবা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর-ফেরত একদল বুভুক্ষু। কুম্ভীর মিয়াঁ এক গালে এক ডজন লুচি ও এক গালে এক ডজন গুড়ের সন্দেশ পুরিয়া মুখ-সঞ্চালনবিদ্যার যে অদ্ভুত আর্ট দেখাইতেছিল, তাহা দেখিয়া কেহ হাসিতেছিল – কেহ ওই বিদ্যা আয়ত্ত করিবার মকশো করিতেছিল, আর যাহারা রাগিয়া উঠিতেছিল তাহাদেরই মধ্যে একজন খানিকটা নস্য লইয়া কুম্ভীর মিয়াঁর নাকে ঠাসিয়া দিল। কুম্ভীর মিয়াঁ নস্য লইত না। অতএব ইহার পর যে বীভৎস দৃশ্যের সৃষ্টি হইল, তাহা না বলাই ভালো। তাহার মুখ-গহ্বর হইতে লালা-মিশ্রিত সমস্ত লুচি ও সন্দেশ উৎক্ষিপ্ত হইয়া প্রায় সকলের অঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিল। খাওয়া রহিল পড়িয়া, লাফাইয়া যে যেখানে পারিল পলাইল। কিন্তু কুম্ভীর মিয়াঁর হাঁচি আর থামে না। হাঁচিতে, কাশিতে, লালাতে, শিকনিতে মিশিয়া একটা বিতিকিচ্ছি ব্যাপার হইয়া গেল। বিকচ্ছ ও প্রায় দিগ্বসন কুম্ভীর মিয়াঁর ভুঁড়ি হাঁচির বেগে প্রবল বেগে আন্দোলিত হইতে লাগিল, – স্টিমার পার হইয়া যাইবার পর গঙ্গা-বক্ষের বয়া যেমন করিয়া দুলিতে থাকে! চক্ষু ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মতো হইয়া উঠিল। হাঁচি-নিষিক্ত নাসিকা দেখিয়া মনে হইল, যেন কর্তিত খেজুরগুঁড়ি দিয়া রস চোঁয়াইতেছে। কেহ তাহার মাথায় কেহ বা ভুঁড়িতে বদনা বদনা পানি ঢালিতে লাগিল। তরিক ‘সুরা ইয়াসিন’ পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। ‘সুরা ইয়াসিন’ অন্তিম সময়েই শুনাইয়া থাকে এবং ‘আজান’ নামাজের সময় ব্যতীত অন্য সময় দিলে সাধারণত লোকে মনে করিয়া থাকে – কাহারও বাড়িতে সন্তান হইয়াছে। সুতরাং তরিকের ‘সুরা ইয়াসিন’ পড়াতে যত না হাসির সৃষ্টি হইল, আমজাদ তাড়াতাড়ি কাছা খুলিয়া প্রাণপণ চিৎকারে আজান দিতে শুরু করায় সকলে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল!
মোটের উপর, যদি কোনো মাতাল এটাকে একটা তাড়িখানা মনে করিয়া ঢুকিয়া পড়িত তাহা হইলে তাহাকে দোষ দেওয়া চলিত না।
এইবার কুম্ভীর মিয়াঁর রাগিবার পালা। রাগাইয়া গালি খাওয়া মুখরোচক বটে, তবে তাহা লুচি ও গুড়ের সন্দেশ নয়। কাজেই তাহা গলাধঃকরণ করিতে অনেকেরই যথেষ্ট বেগ পাইতে হইল। কিন্তু থাক, আর নয়। মেসে এসব ব্যাপার কিছু নতুন নয়।
আড্ডা যখন ভাঙিল, তখন রাত্রি পাশ ফিরিয়া শুইয়াছে। ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজিল।
বাবুর্চি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং যে যা পারিল দুটো মুখে গুঁজিয়া দিয়া আপন আপন সিটে লম্বা হইয়া পড়িল।
ঘুম আসিল কিনা বলিতে পারি না, কেননা হপ্তা-খানিকের মধ্যেই গ্রীষ্মের ছুটি। প্রায় সব কলেজই বন্ধ হইয়া যাইবে।
শুইয়া শুইয়া তরুণেরা গ্রীষ্মের আর পূজার ছুটির আগে যেসব কথা ভাবে, তাহা আন্দাজ করিলে – তরুণেরা যাই হউন, রুচিবাগীশ কুঞ্চিত-নাসিকার দল খুশি হইবেন না। তাঁহারা ভাবিতে পারেন, ছেলেরা সেসময় ভগবৎচিন্তা করে মনে মনে। ইহাও হয়তো বলে – যেন, খুব ভোরে তার ঘুম ভাঙিয়া যায় – সে ফজরের নামাজ পড়িবে! তাঁহাদের এরূপ ভাবায় সমবেদনা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু তরুণেরা তাহা ভাবে না। সকলের কথা বলিতে পারি না, তবে অধিকাংশ তরুণই সেসময় আমতলা, পুকুর-ঘাট, নদীরপাড় এবং আনুষঙ্গিক মধুর আরও কিছুর স্মৃতি – এই সবই হয়তো বিশেষ করিয়া ভাবে।
কাজেই ঘুম সে রাত্রে কাহার আসিল জানি না; অন্তত উলঝলুল ও হারুণের আসে নাই।
সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন যে কামরাটি এবং যাহাতে একটি মাত্র সিট ছিল, সেই কামরাটিতে উলঝলুল একা থাকিত। আড্ডা যখন ভাঙিয়া গেল এবং মেস শান্ত হইল, তখন হারুণ তাহার তক্তা প্যাঁটরা টানিয়া উলঝলুলের স্বল্পায়তন কামরাটির অবকাশটুকু ভরাট করিয়া ফেলিল। উলঝলুল প্রায় গোপাল-কাছা হইয়া চিৎপটাং দিয়া শুইয়া ধূম্রমার্গে বিচরণ করিতেছিল। সে হারুণের তক্তা টানার ঘেসড়ানিতে সচকিত হইয়া উপুড় হইয়া শুইয়া হারুণের কার্যকলাপ দেখিতে লাগিল। দেখিয়া খুব বেশি বিস্মিত হইল বলিয়া মনে হইল না। একরাশ উচ্ছৃঙ্খল কেশের গুচ্ছ ললাট হইতে তুলিয়া সে একটু হাসিল মনে হইল। হারুণও তাহা দেখিয়া ঈষৎ হাসিল।
বাহির তখন শব্দহীন। ক্বচিৎ মোটরের চাকার ঘর্ঘরধ্বনি সেই শব্দহীন অতলতায় নিমেষের জন্য চঞ্চলতার দোলা দিয়া মিলাইয়া যাইতেছিল, – নিশীথ-রাতে তীরের তরুশাখা হইতে একটি ছোট্ট ফল পড়িয়া দিঘির নিতলতায় যেমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। আকাশে অগণিত নক্ষত্র ফেনাইয়া উঠিতেছিল ছায়াপথের কূলে কূলে। ওরা যেন জ্যোতির্ভ্রমর, আকাশ যেন নীলোৎপল, চাঁদ যেন তাহার পদ্মচাকি।
নীরব নিস্পন্দ জগৎ। রাতের চোখে নিদ্রা যেন জড়াইয়া ধরিয়াছে। এমনই নীরব-নিশীথে যদি হৃদয়ের সান্নিধ্য হৃদয় দিয়া অনুভব করা যায়, তবে সে নিশীথ যেন জীবনে আর না কাটে।
কলিকাতার সকল রাজপথ সকল অলিগলির ধুলা-কাদা পায়ে লাগিয়াছে বলিয়াই হতভাগ্য জাহাঙ্গীর আজ উলঝলুল নামের বিদ্রুপ-তিলক পরিয়াছে। অগ্ন্যুৎপাতের ভস্মরাশির মধ্য হইতে মানুষকে টানিয়া বাহির করিবার – বাঁচাইবার দুরন্ত সাধনা তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে বলিয়া, সত্যকে দর্পণের মতো হাতে ধরিয়া দেখিতে চায় বলিয়া সে আজ রুচিবাগীশ নীতি-কচকচিদের ঘৃণার বক্র ইঙ্গিত সহিয়া যাইতেছে। – হারুনের চোখে জল আসিল। সে কিছুতেই নিজেকে সংবরণ করিতে পারিতেছিল না। সে হঠাৎ উলঝলুলকে স্পর্শ করিয়া বলিয়া উঠিল, ‘ওগো সত্যব্রত, ওগো বেদনা-সুন্দর, ওগো পাগল, তোমায় সালাম, হাজারবার সালাম, করি!’ উলঝলুল তখন অঘোর ঘুমাইতেছে!
বাহিরে তাকাইয়া হারুণের মনে হইল সারা আকাশ বাতাস যেন ঘুমাইয়া চাঁদের স্বপন দেখিতেছে! পবিত্র শান্তিতে তাহার হৃদয় স্নিগ্ধ হইয়া গেল। সে ঘুমের ক্ষীরসাগরে ডুবিয়া গেল।
আকাশ, চন্দ্র ও তারকা সাক্ষী রহিল… আজ একটি হৃদয় আর একটি হৃদয়ের সান্নিধ্য লাভ করিল – শুধু হাসি বদল করিয়া…
ধরা আজ সুন্দরতর হইল।
কুহেলিকা – ০২
মেসে যা-ই বলিয়া ডাকুক, আমরা উলঝলুলকে জাহাঙ্গীর বলিয়াই ডাকিব।
জাহাঙ্গীরের পৈতৃক বাড়ি কুমিল্লা জেলায়। তবে সে কলিকাতায় থাকিয়াই মানুষ হইয়াছে। তাহার পিতা ছিলেন কুমিল্লার একজন বিখ্যাত জমিদার ও মানীলোক। বৎসর চারেক হইল, তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সে-ই এখন তাঁহার বিপুল জমিদারির উত্তরাধিকারী। তবে তাহার মাতা আজও জীবিতা, এবং জমিদারি পরিচালনা করেন তিনিই। তাঁহার জমিদারি পরিচালনের অতিদক্ষতা দর্শনে লোকে নাকি বলাবলি করে যে, মেয়েরা সুযোগ পাইলে জমিদারি তো চালাইতেই পারে, কাছা আঁটিয়া ঘোড়ায়ও চড়িতে পারে! তাঁহার শাসনে বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল না খাক, তাঁহার জমিদারির বড়ো বড়ো রুই-কাতলা ও চুনোপুঁটি এক জালে বদ্ধ হইয়া একসাথে নাকানি-চুবানি হইয়াছে। হিন্দু প্রজারা তাঁহাকে বলিত ‘রায়বাঘিনী’ এবং মুসলমানেরা বলিত ‘খাঁড়ে দজ্জাল’ (খরে দজ্জাল)!
জাহাঙ্গীরের পিতা বাঁচিয়া থাকিতে তাহার পিতা-মাতা বৎসরের অধিকাংশ সময় কলিকাতাতেই কাটাইয়াছেন। তাহাদের দু-চারখানা বাড়িও ছিল কলিকাতায়। কিন্তু তাহার পিতার মৃত্যুর পর জাহাঙ্গীরের মাতা সে সমস্ত ভাড়া দিয়া ছেলেকে বেকার হোস্টেলে রাখিয়া নিজে জমিদারি দেখিতে কুমিল্লা চলিয়া যান।
জাহাঙ্গীরের ধাতে কিন্তু হোস্টেলের জেল কয়েদির জীবন সহিল না। সে হোস্টেল ছাড়িয়া মেসে আসিয়া আস্তানা গাড়িল।
ইচ্ছা করিলে সে হয়তো আলাদা বাসা বাঁধিয়াই থাকিতে পারিত, কিন্তু কেন যে তাহা করিল না, তাহা তাহার বিধাতাপুরুষই জানেন। সে মাসে সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিলেও হয়তো তাহার মাতা বিশেষ আপত্তি করিতেন না, তাঁহার অপত্য স্নেহ এতই প্রবল ছিল; কিন্তু জাহাঙ্গীর কোনো মাসে এক শত টাকার বেশি খরচ করিয়াছে, এ বদনাম স্টেটের অতি কৃপণ দেওয়ানজিও দিতে পারেন নাই। ইহাতে জাহাঙ্গীরের মাতা খুশিই হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার খাওয়া-পরার অতিমাত্রায় সাধাসিধে ধরন তাঁহাকে পীড়া দিত। অত বড়ো স্টেটের ভাবী মালিক, সে যদি সংসারে এমনই বীতশ্রদ্ধ হইয়া থাকে এবং এমন মুসাফিরি হালে চলাফেরা করে, তবে কাহার জন্য এ পণ্ডশ্রম? কিন্তু ইহা লইয়া পুত্রকে অনুরোধ বা অনুযোগ করা বৃথা। তাঁহার উপরোধে বা আদেশে জাহাঙ্গীর বরং ঢেঁকি গিলিবার চেষ্টা করিবে, তবু তাহার চলাফেরার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতে দিবে না।
বহুদিন হইতেই জাহাঙ্গীরের চোখে মুখে, চলাফেরায়, কঠিন জীবনযাপনের মধ্যে মাতা এই বিরস ঔদাসীন্য, বেদনাসিক্ত অশ্রদ্ধা দেখিয়া আসিতেছেন এবং তিনি তাহার কারণও জানিতেন, তাই মা হইয়াও তিনি পুত্রকে দস্তুর মতো ভয় করিয়া চলিতেন। তিনি যেন পুত্রের কেউ নন। মাতা-পুত্রের মধ্যে এই দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধানের সৃষ্টি ইতিপূর্বে হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু জাহাঙ্গীর এখন আর বাহিরের দিক দিয়া সহজে তাহা ধরা পড়িবার অবকাশ দেয় না। সে বলে, ‘কী করব মা, আমার স্বভাবই এই, কিচ্ছু ভালো লাগে না যেন।’ সে বলে বটে হাসিয়াই, কিন্তু তাহার পীড়িত মনের চাপ মুখের মুকুরে ধরা পড়ে।
জননী অশ্রু সংবরণ করিয়া উঠিয়া যান। তাঁহার এ দুর্বলতার একটু ইতিহাস আছে। তাহাই বলিতেছি।–
জাহাঙ্গীর যখন ‘জননী ও জন্মভূমিকে স্বর্গাদপি গরীয়সী’ বলিয়া সবে মাত্র শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে শিখিয়াছে, সেই সময় অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে সে শুনিল, তাহার মাতা কলিকাতারই এক জন ডাকসাইটে বাইজি এবং তাহার পিতা চিরকুমার! সে তাহার পিতামাতার কামজ সন্তান!
সেই দিন হইতে তাহার চোখে সুন্দর পৃথিবীর রং বদলাইয়া গিয়াছে। তাহার জীবনের আনন্দ-দীপালিকে যেন থাবা মারিয়া নিভাইয়া দিয়াছে। সে মানুষের জীবনের অর্থ নূতন করিয়া বুঝিবার সাধনা করিতেছে!
সে তাহার আদর্শবাদের কাচ দিয়া বাসি পৃথিবীকে সাত-রঙা করিয়া দেখিয়াছে, সহজ মানুষকে আপন-মনের মাধুরী দিয়া বিচিত্রতর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু আজ সে উদ্যতদণ্ড বিচারকের মতো নির্মম, সে এই পৃথিবীর বিচার করিবে! সে আজ সৃষ্টিকে তাহার এই বারবিলাসিনির মতো ব্যবসাদারী সাজসজ্জার ভণ্ডামির জন্য শাস্তি দিবে!
নিষ্ঠুর বজ্রালোকে আজ সত্যের সহিত তাহার মুখোমুখি পরিচয় হইয়া গিয়াছে। আজ সে কঠোর বাস্তবব্রতী!…
কুহেলিকা – ০৩
তখন স্বদেশযুগের বান ডাকিয়াছে। ইংরেজ তাহার রাজত্ব ভাসিয়া যাওয়ার ভয় না করিলেও ডুবিয়া যাওয়ার আশঙ্কা একটু অতিরিক্ত করিয়াই করিতেছিল। ঘরের ঘটিবাটি সে সামলাইতেছিল না বটে, কিন্তু বাঁধ সে ভালো করিয়াই বাঁধিতেছিল। জাহাঙ্গীর তখনও বালক, – স্কুলে পড়ে। এমনই দিনে ‘জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী’ মন্ত্রে এই কল্পনাপ্রবণ কিশোরকে দীক্ষা দিলেন তাহারই এক তরুণ স্কুলমাস্টার প্রমত্ত। প্রমত্ত যে বিপ্লববাদী, এ ভীষণ সংবাদ স্কুলের কয়েকটি বিপ্লবপন্থী ছাত্র ব্যতীত হয়তো বিধাতাপুরুষও জানিতেন না। তবে সি.আই.ডি. প্রভু জানিতেন কি না, বলা দুষ্কর। বিধাতাপুরুষে আর সি.আই.ডি. মহাপুরুষে এইটুকু তফাত! যাহা পূর্বোক্ত পুরুষের অগোচর, তাহা শেষোক্ত মহাপুরুষের নখদর্পণে! – এক দিন একটি ছাত্র গান করিতেছিল – ‘নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে!’
প্রমত্ত হাসিয়া বলিল, ‘এ গান কাকে উদ্দেশ করে লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ, জানিস?’ ছেলেটি উৎসাহের সহিত বলিয়া উঠিল, ‘কেন স্যার, ভগবানকে উদ্দেশ করে।’ প্রমত্ত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ‘উঁহু, তুই জানিসনে। রবীন্দ্রনাথ শ্রীমৎ টিকটিকি বাবাজিকে স্মরণ করে ভক্তিভরে এ-গান রচনা করেছিলেন।’ ছেলেদের উৎসাহ দেখে কে! সেইদিন হইতে কাহাকেও টিকটিকি বলিয়া সন্দেহ হইলেই, এমনকি দেয়ালে টিকটিকি দেখিলে, তাহারা তারস্বরে গাহিত, –
‘নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে, রয়েছ নয়নে নয়নে।’
প্রমত্তকে ছাত্রদের সকলে শ্রদ্ধা করিত, ভালোবাসিত – ভালো শিক্ষক বলিয়াই নয়, সে সকলকে অন্তর দিয়া ভালোবাসিতে জানিত বলিয়া। উঁচু ক্লাসের অধিকাংশ ছাত্রই তাহাকে প্রমতদা বলিয়া ডাকিত।
প্রমত্তের – একা প্রমত্তের কেন, যে কোনো বিপ্লবনায়কেরই – কোনো কার্যের কারণ জিজ্ঞাসার অধিকার কোনো বিপ্লববাদীরই ছিল না, তবুও তাহারা প্রমত্তের জাহাঙ্গীরকে ‘মাতৃমন্ত্রে’ দীক্ষা দেওয়া লইয়া একটু চড়া রকমেরই প্রতিবাদ করিল। প্রমত্ত কোনো বড়ো দলের নায়ক ছিল না। তবুও তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিবার সাহস বড়ো বড়ো বিপ্লব-নায়কদেরও হয়নি। ভবিষ্যতে প্রমত্ত এক জন বড়ো বিপ্লবনায়ক হইবে, এ-ভয়ও দলের ছোটো-বড়ো দলের সকলেই করিত। সুতরাং এ-প্রতিবাদের উত্তর সে তাহারই অধীন বিপ্লববাদীদের না দিলেও পারিত, কিন্তু লোকটি আসলে ছিল একটু বেশি রকমের ভালো-মানুষ! কাজেই নিয়ম-বিরুদ্ধ হইলেও সে ইহা লইয়া বেশ একটু তর্ক করিল। বলিল, ‘দেখো, আমাদের অধিনায়ক বজ্রপাণি মহাশয়কে আমি আমার ভগবানের চেয়েও শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাঁর এমতকে মানতে যথেষ্ট ব্যথা পাই যে বাংলার মুসলমান ছেলে বিপ্লববাদীর আদর্শকে গ্রহণ করতে পারে না। অবশ্য, তাঁর স্পষ্ট নিষেধ থাকলে আমি জাহাঙ্গীরকে এ দলে নিতে পারতাম না। তা সে যত ভালো ছেলেই হোক। তোমরা বলবে, অধিকাংশ মুসলমান ছাত্রই হয় চাকুরি-লোভী, না হয় ভীরু। কিন্তু ওদের সব ছেলেই যে ওই রকমের, তা বিশ্বাস করবার তো কোনো হেতু দেখিনে। তাছাড়া, আমরা ওদের চেয়ে কম চাকুরি-লোভী, কম ভীরু – এ বিশ্বাস করতে আমার লজ্জা হয়।
দেশপ্রেম ওদের মধ্যে জাগেনি – ওদের কেউ নেতা নেই বলে। আর, ধর্ম ওদের আলাদা হলেও এই বাংলারই জলবায়ু দিয়ে তো ওদেরও রক্ত-অস্থি-মজ্জার সৃষ্টি। যে-শক্তি যে-তেজ যে-ত্যাগ তোমাদের মধ্যে আছে, তা ওদের মধ্যেই বা থাকবে না কেন? তা ছাড়া আমি মুসলমান ধর্মের যতটুকু পড়েছি, তাতে জোর করেই বলতে পারি যে, ওদের ধর্ম দুর্বলের সান্ত্বনা “অহিংসা পরমধর্ম”কে কখনও বড়ো করে দেখেনি! দুর্বলেরা অহিংসার যত বড়ো সাত্ত্বিক ব্যাখ্যাই দিক না কেন, ও জিনিসটা মুসলমানেরা অভ্যাস করেনি বলে ওতে ওদের অগৌরবের কিছু নাই!
আজকাল এক দল অতিজ্ঞানী লোক বীর-ধর্ম রাজসিকতাকে বিদ্রুপ করে তাদের কাপুরুষতার তামসিকতাকে লুকোবার চেষ্টা করছে, কিন্তু আমি তাঁদের জিজ্ঞেস করি – শুধু কি বুদ্ধ খ্রিস্ট নিমাই-ই বেঁচে আছেন বা থাকবেন? রাম, কৃষ্ণ, অর্জুন, আলেকজান্ডার, প্রতাপ, নেপোলিয়ন, গ্যারিবল্ডি, সিজার – এঁরা কেউ বেঁচে নেই – না থাকবেন না? কত ব্যাস-বাল্মীকি-হোমার অমর হয়ে গেলেন এই গাথা লিখেই। তোমরা হয়তো বলবে, অনাগত যুগে এদের কেউ বড়ো বলবে না, কিন্তু তোমাদের সে অনাগত যুগ আসতে আসতে পৃথিবীর পরমায়ু ফুরিয়ে যাবে। তা ছাড়া সাত্ত্বিক ঋষিরা, অহিংস কবিরা অনাগত যুগের অবতারের যে কল্কি বা মেহেদি মূর্তির কল্পনা করেছেন, তাকে তো নখদন্তহীন বলা চলে না। যাক, কী বলতে কী সব বলছি। দ্যাখ, নেংটি-পরা বাবাজিদের এই অহিংসবাদ আমায় এত আহত করে তোলে যে তখন আর আমার কাণ্ডজ্ঞান থাকে না! আমি বলছিলাম কী–’
ইহারই মধ্যে একটি টলস্টয়-ভক্ত ছিলে বলিয়া উঠিল, ‘কিন্তু প্রমতদা, আমরা মার খেয়েই মারকে জয় করব – এ কি একেবারেই মিথ্যা?’
প্রমত্ত উত্তেজিত স্বরে বলিল, ‘তা হলে আমরা বহুদিন হল জয়ী হয়ে গেছি! কারণ, আমরা নির্বিকার চিত্তে এত শতাব্দী ধরে এত মার খেয়েছি যে, যারা মেরেছে তারাই শেষে দিকশিক মেরে গেছে। আমাদের আর্য মেরেছে, অনার্য মেরেছে, শক মেরেছে, হূন মেরেছে! আরবি ঘোড়া মেরেছে চাঁট, কাবলিওয়ালা মেরেছে গুঁতো, ইরানি মেরেছে ছুরি, তুরানি হেনেছে তলওয়ার, মোগল-পাঠান মেরেছে জাত, পর্তুগিজ-ওলন্দাজ-দিনেমার-ফরাসি ভাতে মারতে এসে মেরেছে হাতে, আর সকলের শেষে মোক্ষম মার মেরেছে ইংরেজ। মারতে বাকি ছিল শুধু মনুষ্যত্বটুকু – যার জোরে এত মারের পরও এ জাত মরেনি – তাই মেরে দিলে ইংরেজ বাবাজি! এত মহামারির পরও যদি কেউ বলেন, “আমরা এই মরে মরেই বাঁচছি”, তবে তাঁর দর্শনকে আমি শ্রদ্ধা করি – কিন্তু বুদ্ধিকে প্রশংসা করিনে। তাঁর বুদ্ধি-স্থানের ভালো করে চিকিৎসা হওয়া উচিত। যাক, এ নিয়ে আমাদের আলোচনা নয়। আমি বলছিলাম, সত্যিই কি আমাদের এ আন্দোলন থেকে মুসলমানদের বাদ দেব? ওদের অনেক দোষ আছে স্বীকার করি, কিন্তু ওরা সরল-বিশ্বাসী ও দুঃসাহসী! ওদের হাতে বাঁশ আছে সত্যি, কিন্তু তা ওরা পেছনে লুকিয়ে রাখতে জানে না, একেবারে নাকের ডগায় উঁচিয়ে ধরে – এই যা দোষ। ওতে আমাদের কাজ হয় না। ওদের গুপ্তি-মন্ত্রে দীক্ষা দিলে হয়তো ভাবীকালে সেরা সৈনিক হতে পারত।’
প্রমত্ত কী যেন ভাবিতে লাগিল। মনে হইল, ভাবীকালের দুর্ভেদ্য অন্ধকারে সে ক্ষীণ দীপশিখা লইয়া কী যেন হাতড়াইয়া ফিরিতেছে!
জাহাঙ্গীরের প্রিয়বন্ধু অনিমেষ বলিয়া উঠিল, ‘প্রমতদা, জাহাঙ্গীরকে আমাদের দলে নেওয়ায় অন্তত আমার কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। সে হিন্দু কি মুসলমান, তা ভেবে দেখিনি! তাকে আমি দেখেছি মানুষ হিসাবে! সে হিসাবে সে আমাদের সকলের চেয়েই বড়ো। কিন্তু এ নিয়ে শেষে আমাদের মধ্যে একটা মনান্তর বা বাধে। আমরা বিপ্লববাদী, কিন্তু গোঁড়ামিকে আজও পেরিয়ে যেতে পারিনি – ধর্মকে বাদ দিয়ে মানুষকে দেখতে শিখিনি। এর জন্যে দায়ী আমাদেরই প্রতিদ্বন্দ্বী আর-এক বিপ্লব-সংঘের অধিনায়ক। আপনি বোধ হয় বুঝেছেন প্রমতদা, আমি কাকে মনে করে একথা বলছি!’ প্রমত্ত ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হাসিল। অনেকেই সে-হাসির অর্থ বুঝিল না।
অনিমেষ বলিয়া যাইতে লাগিল, ‘তিনি এবং তাঁর দল কী বলেন, জানেন? বলেন, “আমরা ডান হাত দিয়ে তাড়াব ফিরিঙ্গি এবং বাম হাত দিয়ে খেদাব নেড়ে! সন্ধি করব লন্ডন এবং মক্কা অধিকার করে!” – তারা মুসলমানকে ইংরেজের চেয়ে কম শত্রু মনে করে না!’
প্রমত্ত হাসিয়া বলিল, ‘আর ওই অধিনায়ক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত করে বিলেত ও মক্কা থেকে কী আনবেন – বলতে পারিস?’
ছেলেরা এক বাক্যে স্বীকার করিল, তাহারা বলিতে পারে না।
প্রমত্ত বলিল, ‘তিনি বিলেত গেলে হয়ে আসবেন ট্যাসু, খেয়ে আসবেন হ্যাম, নিয়ে আসবেন মেম। আর মক্কা গেলে হয়ে আসবেন হাজি, খেয়ে আসবেন গোশত এবং নিয়ে আসবেন দাড়ি! সন্ধিপত্র আর আনতে হবে না!’
ছেলেরা হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল। প্রমত্ত বলিয়া যাইতে লাগিল, ‘দেখ, এই বাংলাদেশে গাঁজার চাষ করে গভর্মেন্ট তত সুবিধে করতে পারেনি, যত সুবিধে তাদের করে দিয়েছে আমাদের মহাপুরুষেরা আমাদের মস্তিষ্কে ধর্মের চাষ করে, আমাদের দাঁতের গোঁড়া ভাঙবার জন্যে ইংরেজের শিল নোড়া হয়ে উঠেছে আমাদের ধর্ম। – ইংরেজের ভারত-শাসনের বড়ো যন্ত্র কী, জানিস? আমাদের পরস্পরের প্রতি এই অবিশ্বাস, পরস্পরের ধর্মে আন্তরিক ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা! এই ভেদ-নীতিই ইংরেজের বুটকে ভারতের বুকে কায়েম করে রাখলে – “আদম্স পিকে” আদমের পদচিহ্ন যেমন অক্ষয় হয়ে রইল।’
সমরেশ একটু অতিরিক্ত হিন্দু। সে বলিয়া উঠিল, ‘আচ্ছা প্রমতদা মুসলমানকে বাদ দিয়েও তো আমরা স্বাধীন হতে পারি।’
প্রমত্ত বলিল, ‘নিশ্চয়, অনেক দেশই তাদের স্বদেশবাসীর অন্তত বারো আনা লোকের বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও স্বাধীন হয়েছে; কিন্তু আমরা তা পারব না। কেউ যদি পারে ইংরেজ ও মুসলমানকে একসাথে তাড়াতে, তাড়াক। অন্তত আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই। তবে অন্য যেসব দেশ স্বাধীন হয়েছে, তারা স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধাচরণ সহ্য করেছিল – তাদের তাড়াবার পাগলামি তো তাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করেনি।
যে বিপ্লবাধিপ বলেন – আগে মুসলমানকে তাড়াতে হবে, তিনি ভুলে যান যে তাঁর এ অতিক্ষমতা যদি থাকতও, তা হলেও চতুর ইংরেজ প্রাণ থাকতে তা হতে দিত না। যেদিন ভারত এক জাতি হবে সেইদিন ইংরেজকেও বোঁচকা-পুঁটলি বাঁধতে হবে। এ কথা শুধু যে ইংরেজ জানে তা নয়, রামা শ্যামাও জানে। “হিন্দু” “মুসলমান” এই দুটো নামের মন্ত্রৌষধিই তো ইংরেজের ভারত-সাম্রাজ্য রক্ষার রক্ষা-কবচ। … আমার কিন্তু মনে হয় কী, জানিস? ইচ্ছা করলে আমরা অনায়াসে এদেশের মুসলমানদের জয় করতে পারি। তবে তা তরবারি দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে। অন্তত একটা স্থূল রকমের শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে ওদের পরিচিত না করে তুললে, “কালচার”-এর সংস্পর্শে না আনলে ওদের জয় করতে পারব না। ওদের জয় করা বা স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ করা মানেই ইংরেজের হাতের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া!’
সমরেশ বলিল, ‘কিন্তু প্রমতদা, ওদের গোঁয়ার্তুমি আর আবদারের যে অন্ত নেই। মানি, ওরা ইংরেজের হাতের অস্ত্র, আমরা দেশের কিছু করতে গেলেই মামারা দেবে ওদের লেলিয়ে! কিন্তু উপায় কী? “কনসেশন” দিয়ে দিয়ে ওদের তৃতীয় রিপুটাকে প্রচণ্ড করে তোলায় আমাদের যা হবার তা তো হবেই, ওদের নিজেদেরও চরম অকল্যাণ হবে। ওরা নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা কোনোদিনই করবে না!’
প্রমত্ত – ‘কনসেশন আমিও দিতে বলিনে। আমিও বলি, সমর-যাত্রার অভিযানের সাথি যদি খোঁড়া হয়, তবে তাকে বয়ে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে পথে ফেলে যাওয়াই কল্যাণকর। কিন্তু অভিযান তো আমাদের শুরু হয়নি সমরেশ! এটা রিক্রুটমেন্টের, কাঁচা সৈনিক-সংগ্রহের যুগ – আমরা স্রেফ প্রস্তুত হচ্ছি বই-তো নয়। অনাগত অভিযানের সৈনিক ওরাও হতে পারে কিনা – তা পরীক্ষা করে দেখলে আমাদের দেশোদ্ধারের তারিখ এগিয়ে না যাক, অন্তত পিছিয়ে যাবে না। এখনই তুমি বলছিলে ওদের গোঁয়ার্তুমি আর আবদারের কথা। এ কথা একা তুমি নয়, আমাদের অনেক নেতাই বলছেন! কিন্তু রোগ নির্ণয় করলেই তো রোগের চিকিৎসা হল না। তর্কের কাতিরে মেনে নিলাম – ওরা অতিমাত্রায় আবদেরে, ওরা হয়তো ইংরেজ রাজ্যটাকে মামাবাড়িই মনে করে। কিন্তু এর মূলে কতদিনের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অশিক্ষা পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে – তা দেখেছ কি? সেই কথাই তো বলছিলাম যে, এইগুলো আমাদের সাধনা দিয়ে, তপস্যা দিয়ে দূর করতে হবে। আমাদের ছড়িয়ে পড়তে হবে ওদের মধ্যে ওদের শিক্ষিত করে তোলার জন্যে, ওদের রক্তে স্বদেশপ্রেম জাগিয়ে তোলার জন্যে। দেখবে, আজ যারা তোমার প্রতিবন্ধক, কাল সে তোমার সবচেয়ে বিশ্বাসী ও বড়ো সহযোগী হয়ে উঠবে। ওদের ঘৃণা করে খেপিয়ে না তুলে ভালোবেসে দেখতে দোষ কি?’
সমরেশ – ‘কিন্তু প্রমতদা, ওদের মোল্লা-মউলবিরা তা কখনও হতে দেবে না। জানি না, হয়তো বা ওদের মউলবি-মোল্লা এবং আমাদের ধর্মধ্বজরা ইংরেজের গুপ্তচর। ওরা তখন সাধারণ মুসলমানদের এই বলে খেপিয়ে তুলবে যে, ওদের হিন্দু করে তোলার জন্যই আমাদের এই অহেতুকি মাথাব্যথা। আমাদের এ “নিরুপাধিক” প্রেমচর্চাকে তারা বিশ্বাস করবে না, শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করবে না।’
প্রমত্ত – ‘আমি তাও ভেবে দেখেছি। জানি, মুসলমান জনসাধারণের অভ্যুত্থানে সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি হবে মোল্লা-মউলবির। তাদের রুটি মারা যাবে যাতে করে, তাকে তারা প্রাণপণে বাধা দেবেই। কিন্তু এ ভূতেরও ওঝা আছে, – সে হচ্ছে মুসলমান ছাত্রসমাজ। তরুণ মুসলিমকে যদি দলে ভিড়াতে পারি, তা হলে ইংরেজ আর মোল্লা-মউলবি এ দুই জোঁকের মুখেই পড়বে চুন। এই জন্যই আমি বেছে বেছে মুসলমান ছাত্র নিতে চাই আমাদের দলে এবং এইখানেই আমার সঙ্গে অন্যান্য বিপ্লব-নেতার বাধে খিটিমিটি।’
সমরেশ – ‘আপনার ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির প্রশংসা করি প্রমতদা, কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান ছাত্রই জাহাঙ্গীর তো নয়ই, জাহাঙ্গীরের ভূতও নয়। তারা মনে করে, আমাদের স্বদেশি আন্দোলন মানে হিন্দুরাজের প্রতিষ্ঠা, কাজেই তারা এতে যোগদান করাকে মনে করে পাপ। তারাও সব হা-পিত্যেশ করে তীর্থের কাকের মতো আরব-কাবুল-ইরান-তুরানের দিকে চেয়ে আছে – কখন ওই দেশের মিয়াঁ সাহেবরা এসে ভারত জয় করে ওদের ভোগ করতে দিয়ে যাবে। ওরা ভুলে যায় নাদির শা তৈমুরের কথা!’
প্রমত্ত – ‘মুসলমানেরা যদি হিন্দুরাজের ভয় করেই, তাতে তাদের বড়ো দোষ দেওয়া চলে না সমরেশ! মাতৃ-সমিতির অধিনায়কদের মতও নাকি হিন্দুরাজেরই প্রতিষ্ঠা। তাদের এ ভয় আমাদের আন্তরিকতা, বিশ্বাস ও ত্যাগ দিয়ে দূর করতে হবে। নইলে পরাধীন ভারতের মুক্তি নেই। মাতৃ-সমিতির মতো আমাদের সংঘেও যদি ওই মত হত যে মুসলমানকে এ দেশ থেকে তাড়াতে হবে, তা হলে দেশকে যতই ভালোবাসি না কেন, এ সংঘে আমি যোগদান করতাম না। মুসলমানদের যদি কোনো দোষত্রুটি থাকেই, তবে তার সংশোধনের সাধনা করব। তাদের তাড়াবার পাগলামি যেন আমায় কোনোদিন পেয়ে না বসে। আর, ইরান তুরানের দিকে যে ওরা চেয়ে আছে, তাতে ওদের খুব বেশি দোষ দেওয়া চলে না। দুর্বল মাত্রেই পরমুখাপেক্ষী। নিজেদের শক্তি নেই, ওরা তাই অন্য দেশের মুসলমানদের পানে চেয়ে তাদের শক্তিহীনতার গ্লানিতে একটু সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে; – যদিও ওরা নিজেরাই জানে যে ওদের জন্যে ইরান তুরান আরব কাবুল কারুরই কোনো মাথাব্যথা নেই। আমাদের সাধনা হবে – ওদের ওই পরদেশমুখী মনকে স্বদেশের মমতা দিয়ে ভিজিয়ে তোলা। যে মাটি ওদের ফুলে ফলে শস্যে জলে জননীর অধিক স্নেহে লালন-পালন করছে, সেই সর্বংসহা ধরিত্রীর, মূক মাটির ঋণের কথা তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। তাদের রক্তে এই মন্ত্র জ্বালা করে ফিরবে যে জননীর স্তন্যপানের যদি কোনো ঋণ থাকে, তবে তারও চেয়ে বড়ো ঋণ আমাদের দেশজননীর কাছে – যার জলবায়ু ও রসধারায় আমাদের প্রাণ-মন-দেহ অনুক্ষণ সঞ্জীবিত হয়ে উঠছে – যে দেশ আমার পিতার জননী, আমার জননীর জননী!… ওদের রক্তে এ মন্ত্র ইনজেক্ট করতে পারবি তোরা কেউ সমরেশ? সেদিন ভারতের যে রাজরাজেশ্বরী মূর্তি আমি দেখব, তা আমি আজও দেখছি – আজও দেখছি আমার মানস-নেত্রে! গা দেখি সমরেশ, অনিমেষ! শোনা আমায় সেই সঞ্জীবনী-মন্ত্র! শোনা সেই গান –
‘দেবী আমার, সাধনা আমার,
স্বর্গ আমার, আমার দেশ!’
প্রমত্ত চক্ষু বুজিল। তাহার মুদিত চক্ষু দিয়া বিগলিত ধারে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ছেলেরা তাহার পায়ের ধুলায় ললাট ছোঁয়াইয়া গাহিতে লাগিল, –
‘দেবী আমার, সাধনা আমার,
স্বর্গ আমার, আমার দেশ!’
গাহিতে গাহিতে তাহাদেরও চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।
প্রমত্ত সম্মুখে প্রসারিত ভারতবর্ষের প্রাণহীন মানচিত্রকে বারে বারে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতে লাগিল!
সমরেশ প্রমত্তের পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, ‘এতদিন আপনাকে ভুল সন্দেহ করেছি প্রমতদা, যে, হয়তো মুসলমানের প্রতি আপনার কোনো একটা গোপন দুর্বলতা বা আকর্ষণ আছে। সত্যিই আমরা বিপ্লব-সেনা হবার অধিকারী হয়তো আজও হইনি, আজও আমরা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ভারতের সকলকে ভালোবাসতে পারিনি। আমাদের দেশপ্রেম হয়তো স্রেফ উত্তেজনা, হয়তো ত্যাগের বিলাস। হয়তো আমরা গোঁড়ামিরই রক্ষীসেনা – ধর্মের নবতম পান্ডা। আপনি ঠিকই বলেছেন প্রমতদা, আমরা কেউই আজও দেশ-সৈনিক হতে পারিনি।’
অনিমেষ হাসিয়া বলিল, ‘ঠিক বলেছে সমর, আমরা ধর্মের ষাঁড় – বিপ্লবদেবতার কেউ নই!’
প্রমত্ত চক্ষু মুছিয়া সিক্তস্বরে বলিল, ‘আমার ভারত এ-মানচিত্রের ভারতবর্ষ নয় রে অনিম! আমি তোদের চেয়ে কম ভাবপ্রবণ নই, তবু আমি শুধু ভারতের জল বায়ু মাটি পর্বত অরণ্যকেই ভালোবাসিনি! আমার ভারতবর্ষ – ভারতের এই মূক-দরিদ্র-নিরন্ন পর-পদদলিত তেত্রিশ কোটি মানুষের ভারতবর্ষ। আমার ভারতবর্ষ ইন্ডিয়া নয়, হিন্দুস্থান নয়, গাছপালার ভারতবর্ষ নয়, – আমার ভারতবর্ষ মানুষের যুগে যুগে পীড়িত মানবাত্মার ক্রন্দন-তীর্থ। কত অশ্রুসাগরে চড়া পড়ে পড়ে উঠল আমার এই বেদনার ভারতবর্ষ! ওরে, এ ভারতবর্ষ তোদের মন্দিরের ভারতবর্ষ নয়, মুসলমানের মসজিদের ভারতবর্ষ নয় – এ আমার মানুষের – মহা-মানুষের মহা-ভারত!’
কুহেলিকা – ০৪
স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষা লওয়ার কয়েক মাস পরেই জাহাঙ্গীরের পিতা খান বাহাদুর ফররোখ সাহেবের হৃদরোগে মৃত্যু হইল। জাহাঙ্গীর তখন পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক, সবেমাত্র সেকেন্ড ক্লাস হইতে ফার্স্ট ক্লাসে প্রমোশন পাইয়াছে। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় তাহার মনে হইল, সে যেন পথ চলিতে চলিতে সহসা এক ইঁদারার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু যে ভয় সে করিয়াছিল, তাহা হইতে মুক্তি দিলেন আসিয়া তাহার মাতা – ফিরদৌস বেগম। আঁখির অশ্রু না শুকাইতেই তিনি সমস্ত স্টেট পরিচালনের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। জাহাঙ্গীর পরিপূর্ণ মুক্তির আনন্দে একেবারে ছোটো খোকাটির মতো তাহার মায়ের কোলে শুইয়া আদর-আবদারে মাকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। মা অঞ্চলে অশ্রু মুছিয়া পুত্রের ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন, ‘আচ্ছা, এ সবকে যে এত ভয় করিস, আমি মরলে তখন করবি কী বল তো? এত বড়ো জমিদারি তুই না দেখলে আমি মেয়েমানুষ কি একা দেখতে পারব? পাঁচ-ভূতে হয়তো সব চুরি করে খেয়ে নেবে।’ জাহাঙ্গীর সব বুঝিল। তার চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল। সে পিতাকে একটু অহেতুক ভয় করিলেও ভালোবাসিত প্রাণ দিয়া। মায়ের কোলে মুখ লুকাইয়া সে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল; মা বারণ করিলেন না, শুধু গাঢ় স্নেহে পুত্রের মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন – যেন তাহার সমস্ত অকল্যাণ দুই হস্তে মুছিয়া লইবেন!…
পিতা-মাতা জাহাঙ্গীরকে যেন অতিরিক্ত সতর্কতার সহিত রক্ষা করিতেন। জাহাঙ্গীর তাহাকে অতি-স্নেহ ব্যতীত আর কিছু মনে করিতে পারে নাই। সে কিন্তু এতদিন একটু-আধটু বুঝিতেছিল যে, তাহাকে পিতা তাঁহার আত্মীয়দের সাথে মেলামেশা তো দূরের কথা, দেখাশুনা পর্যন্ত করিতে দিতে নারাজ। তাহাদের দেশ ও জমিদারি কুমিল্লায় – কিন্তু আজও সে কুমিল্লা দেখিল না। ছুটি হইলেই তাহার পিতামাতা তাহাকে ওয়ালটেয়ার, পুরী, আগ্রা, ফতেপুর, দিল্লি, লাহোর লইয়া ফিরিতেন। জমিদারি-সংক্রান্ত ব্যাপারে কুমিল্লা আসিতে হইলে ফররোখ সাহেব একাই আসিতেন। স্ত্রী-পুত্র কাহাকেও সঙ্গে লইতেন না।
জাহাঙ্গীর ছেলেবেলা হইতে একটু পাগলাটে ধরনের। লোকে বলিত, ‘বড়োলোকের ছেলে বলেই ইচ্ছা করে ওই রকম পাগলামি করে রে বাবা! বাপের অত টাকা থাকলে আমরাও পাগল হয়ে যেতাম। আদুরে গোপাল, “নাই” পেয়ে বাঁদর হয়ে উঠছে!’ –অবশ্য, বলিত তাহারা গোপনেই এবং তাহারা ফররোখ সাহেবেরই কর্মচারী।
বড়োলোকের ছেলের পাগলামির মধ্যে তবু একটা হয়তো শৃঙ্খলা থাকে – মানে থাকে, কিন্তু জাহাঙ্গীরের চলাফেরা বলা-কওয়ার না ছিল মাথা, না ছিল মুণ্ডু। এই হয়তো বাচালের মতো বকিয়া যাইতেছে, পরক্ষণেই ধ্যানীর মতো অতল নীরবতায় মগ্ন হইয়া গেল। এবং এই রকম নীরব সে দিনের পর দিন থাকিতে পারিত। তাহার এই মগ্নতার দিকটাই প্রমত্তকে এত আকৃষ্ট করিয়াছিল এবং তাই সে জাহাঙ্গীরকে বিপ্লবের গোপনমন্ত্রে দীক্ষা দিতে সাহস করিয়াছিল।…
ইহারই কয়েক দিন পর জাহাঙ্গীর ঝটিকা-উৎপাটিত মহিরুহের মতো মায়ের পদতলে আছাড় খাইয়া পড়িয়া আর্তনাদ করিয়া বলিল, ‘বলো মা, এ কি সত্যি? এ-সব কী শুনি?’
ফিরদৌস বেগম পুত্রের এই অগ্ন্যুৎদ্গার-উন্মুখ আগ্নেয়গিরির মতো ধূমায়মান চোখমুখ দেখিয়া রীতিমতো ভয় খাইয়া গিয়াছিলেন। তাহার মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না। সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করিয়া তিনি কোনো-রূপে শুধু বলিতে পারিলেন, ‘কী হয়েছে খোকা? ও কী, অমন করছিস কেন?’
জাহাঙ্গীর বজ্রকণ্ঠে চিৎকার করিয়া বলিল, ‘বাবার ভাগিনেয়রা সম্পত্তির দাবি করে নালিশ করেছে – আমি-আমি – আমি নাকি জারজ পুত্র, তুমি মুন্না বাইজি – তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী নও – তাঁর রক্ষিতা – আমি খান বাহাদুরের রক্ষিতার পুত্র!’ – কান্নায়, ক্রোধে, উত্তেজনায় জাহাঙ্গীরের কণ্ঠ ক্ষুব্ধ দীর্ণ হইয়া উঠিল! মুখে তাহার ফেনা উঠিতেছিল, লেলিহান অগ্নিশিখার মতো সে জ্বলিয়া উঠিতেছিল! বিদীর্ণ কণ্ঠে সে তাহার জননীর পায়ে মুখ রাখিয়া বলিতে লাগিল – ‘বলো মা, এ মিথ্যা – মিথ্যা! ওরা সব মিথ্যা কথা বলছে! আমি যে সূর্যালোকে আর আমার মুখ তুলতে পারছিনে! মা! মা!’
যাঁহাকে লইয়া এ কেলেঙ্কারি, সেই মা তখন বজ্রাহতের মতো কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন! যেন জীবন্ত তাঁহাকে কে পোড়াইয়া দিয়া গিয়াছে! তাঁহার প্রাণ-দেহ সব যেন এক মুহূর্তের অভিশাপে প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছে!
জাহাঙ্গীর ক্ষিপ্তের মতো উঠিয়া তাহার মাতার হাত ধরিয়া প্রচণ্ডবেগে নাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, ‘বলো – নইলে খুন করব তোমাকে! বলো – তুমি খান বাহাদুরের রক্ষিতা, না আমার মা?’ বলিয়াই সে যেন চাবুক খাইয়া চমকিয়া উঠিল! ও যেন উহার স্বর নয়, ও স্বর উহার পিতার, ও রসনা যেন ফররোখ সাহেবের! তাহার মাঝে তাহার পিতাকে এই সে প্রথম অনুভব করিল! হঠাৎ সে স্তব্ধ হইয়া গেল। তার পর, বিচারকের মতো তীব্র দৃষ্টি দিয়া মাতাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অভিভূতা মাতা শুধু করুণ-কাতর চক্ষে পুত্রের পানে চাহিয়াছিলেন!
জাহাঙ্গীর আর একটিও কথা না বলিয়া মন্ত্র-ত্রস্ত সর্পের মতো মাথা নোয়াইয়া টলিতে টলিতে বাহির হইয়া আসিল। চলিতে চলিতে তাহার মনে হইতে লাগিল, ধরণি যেন তাহার চরণদ্বয় গ্রাস করিতেছে – যেন একটা ভীষণ ভূমিকম্প হইতেছে – দানবী ধরা এখনই বিদীর্ণ হইয়া তাহাকে গ্রাস করিয়া পিষিয়া চিবাইয়া মারিবে!
যাইতে যাইতে শুনিল, মুমূর্ষু ভিখারিনি যেমন করিয়া ভিক্ষা মাগে, তেমনি করিয়া তাহার মাতা ক্ষীণ কণ্ঠে ডাকিতেছেন, ‘ফিরে আয়, ফিরে আয় খোকা, ফিরে আয়!’
জাহাঙ্গীরের প্রাণ যেন তাহারই প্রত্যুত্তরে বলিতে লাগিল, ‘ওরে হতভাগিনি! হয়তো জাহাঙ্গীর আবার ফিরবে, কিন্তু তোর খোকা আর ফিরবে না!’
সে সোজা প্রমত্তের বাসা অভিমুখে চলিতে লাগিল। যাইতে যাইতে সে কেবলই আপনার মনে বলিতে লাগিল, ‘ওগো ধরিত্রী মা, আজ হতে আমি তোমার ক্লেদাক্ত ধূলিমাখা সন্তান – এই হোক আমার সবচেয়ে বড়ো পরিচয়! আজ হতে আমি মানব-পরিত্যক্ত নিখিল-লজ্জিত নরনারীর দলে!… ওগো সর্বংসহা মা, যে বুকে কোটি কোটি জারজ শিশুদের নিয়ে দোলা দিয়েছ, সেই বুকে নিয়ে আমায় দোলা দাও, দোলা দাও! যে স্পর্ধায় কুমারীর পুত্রকে করেছ মহাবীর, মহর্ষি, পয়গম্বর – সেই স্পর্ধার অক্ষয় তিলক আমায় পরাও মা!’…
জাহাঙ্গীর যখন উন্মত্ত মাতালের মতো প্রমত্তের বাসায় আসিয়া পৌঁছিল, তখন মৃত দিবসের পাণ্ডুর মুখ সন্ধ্যার কালো কাফন দিয়া ঢাকা হইতেছে। সান্ধ্য আজান ধ্বনি তাহারই ‘জানাজা’ নামাজের আহ্বানের মতো করুণ হইয়া শুনাইতেছিল। মাথার উপর দিয়া চিৎকার করিতে করিতে ক্লান্ত বায়স উড়িয়া চলিতেছিল – যেন মৃত দিবসের শবযাত্রী। ম্লান আকাশের আহিনায় শুধু একটি তারা ছলছল করিতেছিল ক্ষীণ করুণ করণে – যেন সদ্য পুত্রহীনার চোখ!
প্রমত্ত জাহাঙ্গীরকে দেখিয়া ভয় খাইয়া গেল। সে নিজেদের বিপদের কল্পনা করিয়া বলিয়া উঠিল, – ‘কী রে, কোনো খারাপ খবর আছে না কি?’ জাহাঙ্গীর বলিল, ‘আছে’, – বলিয়াই ঘরে ঢুকিয়া দ্বারে অর্গল দিয়া দিল।
বস্তির মধ্যে খোলার ঘর। যতদূর পরিষ্কার রাখা যায় স্যাঁতসেতে নোংরা ঘরকে, তার চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই; তবু তাহার দীনতা ফুটিয়া বাহির হইতেছে – ঘষামাজা বিগত যৌবনের মতো। ক্ষীণ মৃৎ-প্রদীপালোকে দেখা যাইতেছে শুধু একটি ছিন্ন অজিনাসন ও ভারতের ম্লান মানচিত্র। ধূপ-গুগ্গুলের ধোঁয়ায় আর ভিজে মাটির গন্ধে মিশিয়া ঘরের রুদ্ধ বাতাসকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছে।
প্রমত্ত উদ্বেগ-আর্ত কণ্ঠে বলিল, ‘কোথায় কী হয়েছে, বল তো!’
জাহাঙ্গীর বিরস-কঠোর কণ্ঠে বলিল, ‘দেশসেবার পবিত্র ব্রত আমায় দিয়ে হবে না প্রমতদা।’
প্রমত্ত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ‘যাক যা ভয় করছিলাম, তার কিছু নয় তা হলে! – আবার কার সঙ্গে ঝগড়া করলি?’
জাহাঙ্গীর বলিল, ‘বিধাতার সঙ্গে। আমি এ পবিত্র ব্রত নিতে পারি না প্রমতদা! না জেনে নিয়েছিলাম, তার জন্যে যা শাস্তি দেবেন দিন। আমার রক্ত অপবিত্র – আমি জারজ পুত্র!’ শেষ দিকে জাহাঙ্গীরের কণ্ঠ বেদনায় ঘৃণায় কান্নায় ভাঙিয়া পড়িল।
প্রমত্ত চমকিয়া উঠিল। তাহার পর গভীর স্নেহে জাহাঙ্গীরকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, ‘ যা ভয় করেছিলাম, তাই হল।… যাক ওতে তোর লজ্জার কী আছে বল তো! যদি লজ্জিতই হতে হয় বা প্রায়শ্চিত্তই করতে হয় তো তা করেছে, করবে বা করছে তারা, যারা এর জন্যে দায়ী। কোনো অসহায় মানুষই তো তার জন্মের জন্যে দায়ী নয়!’ – জাহাঙ্গীর যেন পথহারা অন্ধকারে কাহার বলিষ্ঠ হাতের স্পর্শ পাইল – তাহাই সে বজ্রমুষ্ঠিতে ধরিতে চায়।
সে খাড়া হইয়া বসিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিল, ‘সত্যি বলছেন প্রমতদা? আমি তা হলে নিষ্পাপ? পিতার লালসা, মাতার পাপ আমার রক্ত কলুষিত করেনি? করেছে, করেছে! আজ আমি তার পরিচয় পেয়েছি। আমার মাঝে আজ প্রথম আমি আমার পশু-পিতাকে দেখতে পেয়েছি! দেখুন প্রমতদা, আমি জীবনে কখনও কুকথা উচ্চারণ করিনি, কিন্তু আজ আমি এক নারীকে পিতার রক্ষিতা বলে গালি দিয়ে আমার রসনা কলঙ্কিত করেছি; – সে নারী আমারই জন্মদাত্রী! না প্রমতদা আমার প্রতি রক্তকণা অপবিত্র – আমার অণু-পরমাণুতে আমার পিতার কুৎসিত ক্ষুধা, মাতার দূষিত প্রবৃত্তি কিলবিল করে ফিরছে বিছের বাচ্চার মতো – যে কোনো মুহূর্তে তা আত্মপ্রকাশ করতে পারে আজকের মতো। আপনার মহান যজ্ঞে আমার আত্মদান দেবতা গ্রহণ করতে পারেন না প্রমতদা। পাপের যূপকাষ্ঠে আমার বলি হয়ে গেছে।’ জাহাঙ্গীর হাঁপাইতে লাগিল – মনে হইল, এখনই বুঝি তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবে।
প্রমত্ত শান্ত দৃঢ়স্বরে বলিল, ‘আমাদের মন্ত্র তুমি ভুলে যাচ্ছ জাহাঙ্গীর। “জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী” আমাদের ইষ্টমন্ত্র। জননী জন্মভূমির বিচার করবার অধিকার আমাদের নেই।’ – শেষ দিকটা আদেশের মতো শুনাইল।
জাহাঙ্গীর লুটাইয়া পড়িয়া বলিতে লাগিল, ‘মিথ্যা ও মন্ত্র! জননী নয়, জননী নয়, – শুধু জন্মভূমিই স্বর্গাদপি গরীয়সী!’
প্রমত্ত জাহাঙ্গীরকে মায়ের মতো বুকে করিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিল, ‘পাপ যদি তোর থাকেই জাহাঙ্গীর, দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে তোকে খাঁটি নেব, তুই কাঁদিসনে।’
জাহাঙ্গীর তখনও চিত্র-ভারত বুকে ধরিয়া উপুড় হইয়া কাঁদিতেছিল, ‘শুধু তুমি, জন্মভূমি আমার, শুধু তুমি একা স্বর্গাদপি গরীয়সী, – আর কেউ নয়, আর কেউ নয়!’
বুকের তলায় চিত্র-ভারত অশ্রু-সিক্ত হইয়া উঠিল।
কুহেলিকা – ০৫
গ্রীষ্মের ছুটি হইয়া গিয়াছে। ছাত্রদের যৌবনোন্মুখ মন অকারণ সুখে কানায় কানায় পুরিয়া উঠিয়াছে। তাহারা আজ তাহাদের সুদূর পল্লির নব-মুকুলিত আম্রবীথির গন্ধস্বপন দেখিতেছে।
হারুণ বাড়ি যাইবার জন্য সমস্ত গুছাইয়া তাহার খালি তক্তপোশের উপর শুইয়া কী যেন চিন্তা করিতেছিল। তাহার দেশের ট্রেন ছাড়িবার তখনও পাঁচ ছয় ঘণ্টা দেরি। পশ্চাৎ হইতে কাহার কেশাকর্ষণে চমকিয়া উঠিয়া সে দেখিল, জাহাঙ্গীর ওরফে উলঝলুল দাঁড়াইয়া সিগারেট টানিতেছে! হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, ‘তোমার ট্রেন কয়টায় হারুণ?’
হারুণ মৃদু হাসিয়া বলিল, ‘কেন, তুমিও যাবে নাকি আমার সাথে।’
জাহাঙ্গীর পকেট হইতে দুইখানা টিকিট বাহির করিয়া দেখাইল, সে আগেই শিউড়ি পর্যন্ত দুইখানা টিকিট করিয়া রাখিয়াছে।
হারুণ বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া জাহাঙ্গীরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। হঠাৎ সে কণ্ঠে করুণ আবেদন ঢালিয়া বলিয়া উঠিল, ‘কিন্তু তোমার তো সেখানে যাওয়া হতে পারে না ভাই।’
জাহাঙ্গীর গম্ভীরভাবে হাই তুলিয়া তুড়ি মারিয়া আলস্য-জড়িত-স্বরে বলিল, ‘তুমি জান না হারুণ, আমার যাওয়া হবেই, তোমার যদি না-ই হয়।’
হারুণ তাহার বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, ‘তুমি জান না জাহাঙ্গীর, সে কী রকম অজপাড়াগাঁ। সেখানে চামচিকের মতো মশা–’
হারুণ আর কিছু বলিবার আগেই জাহাঙ্গীর কৃত্রিম ভীত স্বরে বলিয়া উঠিল, ‘বাদুড়ের মতো মাছি, বন্য বরাহের মতো ইঁদুর, হারুণের মতো বাঁদর! এই তো, না আর কিছু?’
হারুন হতাশ হইয়া বলিল, ‘সত্যি ভাই লক্ষ্মীটি! তুমি কিছু মনে কোরো না! সেখানে তোমার অসুবিধার একশেষ হবে! সর্বপ্রথম তো, শিউড়ি থেকে পাঁচটি কোশ পথ “শ্রীচরণ মাঝি ভরসা” করে পাড়ি দিতে হবে। মাঝরাস্তায় বক্কেশ্বর নদী –’
জাহাঙ্গীর নিশ্চিন্ত-আরামে সিগারেট টানিতে টানিতে বলিল, ‘সে বৈতরণিতে তরণি নাই, কর্ণধার নাই, ভীষণ স্রোত, স্রোতে ভীষণ হাঙর, কুম্ভীর, তিমি, সর্প, এই তো? কিন্তু আমি জানি হারুণ, এ-সবের একটাও নেই সেখানে। আর যদি থাকেও তবে –
‘আল্লা আল্লা বইল্যা রে বাই নবি কইর্যা সার, মাজা বাইন্দ্যা চইল্যা যাইবাম ভব নদীর পার!’ বুঝলে? অদৃশ্য কর্ণধারকে একেবারে অষ্টরম্ভা দেখিয়ে গোপালকাছা হয়ে উসপার!’
হারুণ এইবার একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া পড়িল। বন্ধু তাহার বাড়ি যাইবে, ইহাতে সে আনন্দিত যেমন হইতেছিল, তেমনই তাহার অসোয়াস্তির আর অন্ত ছিল না তাহার বাড়ির দুরবস্থার কথা ভাবিয়া। উপবাস অবশ্যই সেখানে করিতে হইবে না, কিন্তু জাহাঙ্গীরের মতো এত সুখে লালিতপালিত জমিদার-পুত্রকে যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন করিবার মতো সম্বলও তাহাদের নাই। এই দৈন্যের স্মৃতিই তাহার মনকে পীড়িত করিয়া তুলিতেছিল। অসহায়ের নিষ্ফল ক্রন্দনের বাষ্পে তাহার আঁখি বারেবারে করুণ হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু জাহাঙ্গীরের এই অকপট বন্ধুত্বের সরলতায়, এই আত্মীয়তার দাবিতে তাহার কবি-মন ভিজিয়া উঠিল। এতক্ষণ সে ‘মরিয়া হইয়া’ চেষ্টা করিতেছিল, জাহাঙ্গীরের কিছুতেই যাওয়া হইতে পারে না, কিন্তু এখন আর সে প্রতিবাদ করিল না। উলটো, কেমন এক খুশিতে তাহার সারা মন অভিষিক্ত হইয়া উঠিল। তাহার কল্পনাপ্রবণ হৃদয় সকল কিছু ত্রুটি অভাবকে রঙিন করিয়া দেখিতে লাগিল তাহার সুদূর পল্লি-নীড় যেন তাহার সকল অভাব অপূর্ণতার জন্যই বেশি করিয়া সুন্দর মনে হইতে লাগিল। তাহার স্বাভাবিক বিষন্ন মুখ খুশিতে প্রভাতের ফুলের মতো সুন্দর দেখাইতে লাগিল।
জাহাঙ্গীর ইচ্ছা করিয়াই অতি সাদাসিধে গোটাকতক জামা-কাপড় লইয়া একটা ছোটো বেতের বাক্সে ভরিল। তাহার পর দুই জন এক সঙ্গে স্নান আহার সারিয়া স্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিল। হ্যারিসন রোড ও কলেজ স্ট্রিটের জংশনে টাক্সি আসিতেই জাহাঙ্গীর কী মনে করিয়া হঠাৎ গাড়ি হইতে নামিয়া পড়িল। ট্যাক্সিওয়ালাকে সেইখানে থামিতে বলিয়া হারুণের দিকে তাকাইয়া বলিল, ‘এক্ষুনি আসছি’ বলিয়াই সে কলেজ স্ট্রিট মার্কেট অভিমুখে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।
আধ ঘণ্টা পরে যখন সে মস্ত একটা তোরঙ্গ নিজেই ঘাড়ে করিয়া আসিল, তখন হারুণ যেন কোথায় কোন স্বপ্নলোকে হারাইয়া গিয়াছে। জাহাঙ্গীর তোরঙ্গটা ট্যাক্সিতে দিয়া ট্যাক্সিচালককে যখন যাইতে বলিল, তখনও হারুণ তন্দ্রাবিষ্ট হইয়া কী যেন ভাবিতেছে।
জাহাঙ্গীর হারুণের বাহুতে এক রাম-চিমটি দিয়া গম্ভীরভাবে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সিগারেট ফুঁকিতে লাগিল।
হারুণ প্রায় লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, ‘উহ্ঃ! এ কী! তুমি এলে কখন?’ – বলিয়া বাহুতে হাত বুলাতেই লাগিল।
জাহাঙ্গীর উদাস স্বরে বলিল, ‘জগতে শুধু কবির স্বপ্নই নাই কবি, অ-কবির রাম চিমটিও আছে!’
হারুণ হাসিয়া বলিল, ‘এর পরেও যদি তাতে সন্দেহ প্রকাশ করি, তা হলে হয়তো তুমি ট্যাক্সি থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে বলবে, যে, কবির স্বপ্নলোকের চেয়েও সত্যি এই মাটির পৃথিবীটা এবং ওই মাড়োয়ারি-কণ্টকিত ফুটপাথটা!’
হঠাৎ হারুণ দেখিতে পাইল ট্যাক্সি হাওড়া স্টেশনের দিকে না যাইয়া বাগবাজারের দিকে ছুটিতেছে। সে একটু চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, ‘ওহে জাহাঙ্গীর, এ যে, বাগবাজার এসে পৌঁছলুম আমরা। এখানে হাওড়া স্টেশন পাওয়া যায় নাকি?’
জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, ‘না, এখানে পাওয়া যায় চণ্ডু আর রসগোল্লা।’
হারুণ হাসিয়া বলিল, ‘ বুঝেছি! তুমি আজকাল ওই প্রথম চিজটা একটু বেশি করেই টানছ মনে হচ্ছে।’
ট্যাক্সি এক সন্দেশের দোকানের সামনে আসিয়া থামিতেই জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, ‘দেখলে! ট্যাক্সিরও রসবোধ আছে!’ বলিয়াই সে নামিয়া পড়িল।
হারুণ হতাশ হইয়া বলিল, ‘আজ স্টেশনে বসে বসে ওই মিষ্টিই খেতে হবে। ট্রেন আর পাওয়া যাচ্ছে না।…
গ্রীষ্মের রৌদ্রদগ্ধ মধ্যাহ্ন।….
উল্কাবেগে মাঠ-ঘাট-প্রান্তর বাহিয়া চলিয়াছে ট্রেন। সুখে আলস্যে হারুণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। শুধু জাহাঙ্গীর জানালার বাহিরে মুখ রাখিয়া রৌদ্র-প্রতপ্ত আকাশের চোখে চোখ রাখিয়া চাহিয়া আছে। ট্রেনের প্রচণ্ড গতিবেগকে ছাড়াইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে তাহার মন ওই তাপদগ্ধ আকাশের পানে। সে যেন আকাশের ওই তপ্ত ললাটে ললাট রাখিয়া তাহার ললাটের জ্বালা অনুভব করিবে। মধ্যাহ্নের দীপ্ত সূর্য তখন আগুন বৃষ্টি করিতেছে। তপ্ত চুল্লির সম্মুখে বালিকাবধূর মতো ধরণি এলাইয়া পড়িয়াছে।
জাহাঙ্গীর দুই হাত তুলিয়া ললাট স্পর্শ করিয়া মধ্যাহ্ন-দিনের সূর্যকে নমস্কার করিল। তাহার চক্ষু জলে টইটুম্বুর হইয়া উঠিল। সেই অশ্রুসিক্ত চক্ষু সূর্যের পানে তুলিয়া ধরিয়া সে আপন মনে বলিতে লাগিল, জানি না বন্ধু, তোমার বুকে কীসের এ জ্বালা! কোন অভিমানে তুমি পুড়াইয়া মারিতেছ এই শান্ত ধরণিকে! আমার এ-বুকে তোমারই মতো জ্বালা বন্ধু! কিন্তু সে জ্বালায় জ্বলিয়া আমিও কেন তোমার মতো মধ্যাহ্ন-দিনের সূর্য হইয়া উঠি না? কেন আমার জ্বালা তাহার জ্বালার সাথে আলোও দান করিতে পারে না?
ছোট! ছোট! ওরে যন্ত্ররাজের দুরন্ত শিশু! ছোট তুই আরও – আরও – আরও বেগে! নিয়ে চল একেবারে ওই সূর্যের বহ্নিপিণ্ডের বুকে। চল–চল ওরে ধরার ধূমকেতু। চল ওই জ্বালা-কুণ্ডের হামাম-সিনানে! ঝাঁপাইয়া পড়, যেমন করিয়া কোটি কোটি উল্কাপিণ্ড ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে ওই জ্বালা-কুণ্ডে!
কুহেলিকা – ০৬
শিউড়ি যখন তাহারা পঁহুছিল, তখন রাত্রি বেশ ঘনাইয়া আসিয়াছে।
হারুণ বলিল, ‘এখন, কী করা যায় বলো তো? এখানেই রাত্রিটা কাটিয়ে দেবে না শহরে যাবে! শহরে আমার এক দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় আছেন, যদি তোমার মত হয় সেখানেও যেতে পারি।’
জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, ‘দূর সম্পর্কের আত্মীয়বাড়ির চেয়ে স্টেশনের প্লাটফর্ম ঢের বেশি সোয়াস্তিকর হারুণ। ব্যাস! খোলো গাঁঠরি! এমন চাঁদনি রাত, প্লাটফর্মে শুয়ে দিব্যি রাত্তির কাটিয়ে দেওয়া যাবে। আর, যদি বল রাত্তিরেই তোমার বক্কেশ্বর পাড়ি দিতে হবে, তাতেও রাজি।’
হারুণও হাসিয়া বলিল, ‘বেশ, সেই ভালো। কিন্তু প্লাটফর্মের কাঁকরগুলো সারা রাত্তির হয়তো পিঠের সঙ্গে রসিকতা করবে।’
জাহাঙ্গীর তোরঙ্গটার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, ‘কাঁচকলার কবি তুমি। এমন চাঁদনি রাতের চাঁদোয়ার তলে শুয়েও যে পিঠের তলায় কাঁকরগুলোকে তুলতে পারে না, সে হচ্ছে – কী বলে ইয়ে এই – পাটের দালাল!’
হারুণ হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, ‘এ কীরকম উপমাটা হল?’
জাহাঙ্গীর কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল, ‘ড্যাম ইয়োর উপমা! তোমার ওই উপমার লেসবুনুনি দিয়ে মানুষের মোক্ষলাভ হবে না! যত সব কুঁড়ে আঁস্তাকুঁড়।’
হারুণ বলিল, ‘কিন্তু এই কুঁড়ের আস্তাকুঁড়েই পদ্মফুল ফোটে জাহাঙ্গীর!’
জাহাঙ্গীর সিগারেটের মুখাগ্নি করিতে করিতে বলিল, ‘সে আস্তাকুঁড়ে নয় কবি, সে ফোটে তোমাদের ওই মাথার গোবরে! কিন্তু ও কাব্যালোচনা এখন চুলোয় যাক, এ সিগারেটের ধোঁয়ায় তো আর পেট ভরবে না। পেটের ভিতর যে এদিকে বেড়াল আঁচড়াচ্ছে। তুমি এই সব পাহারা দাও, আমি চললাম খাদ্যান্বেষণে।’
হারুণ কী বলিতে যাইতেছিল, তাহাকে এক দাবড়ানিতে থামাইয়া দিয়া জাহাঙ্গীর চলিয়া গেল। হারুণ নিরুপায় হইয়া প্লাটফর্মে পরিপাটি করিয়া বিছানা পাতিয়া গা এলাইয়া শুইয়া পড়িল।
গ্রীষ্মের সচন্দ্রা যামিনী। তাপদগ্ধ আকাশের নীল দেহে কে যেন গোপী-চন্দন অনুলিপ্ত করিয়া দিয়াছে। রৌদ্রদগ্ধ দিবস, রাত্রির শীতলকোলে মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বাঁদির মতো তরুর সারি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কেবল বীজন করিতেছে।
আবেশে তন্দ্রায় হারুণের চক্ষু জড়াইয়া আসিল। এই দুঃখের অভাবের ধুলার পৃথিবী তাহার স্বপ্নে অপরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠিল। ইহার হাসি যেমন মায়াবী, ইহার অশ্রুও তেমনই জাদু জানে। এই মায়াবিনীকে তাহার একটি ক্ষীণাঙ্গী বালিকার মতো করিয়া বুকে চাপিয়া ধরিতে ইচ্ছা করিল!
হঠাৎ জাহাঙ্গীরের রাম-ঠেলায় সচকিত হইয়া হারুণ উঠিয়া বসিয়া দেখিল, ‘জাহাঙ্গীরের খাদ্যান্বেষণ’ ব্যর্থ হয় নাই। শিউড়ির যাহা কিছু ভালো বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, সে তাহার সব কিছুই চ্যাঙারি বোঝাই করিয়া আনিয়াছে।
হারুণ বলিল, ‘শিউড়ির খবর আমার চেয়ে তুমিই বেশি রাখ দেখছি। তুমি শহরে গিয়ে বুঝি এই সব কাণ্ড করে এলে? কিন্তু এই সব খেয়ে শেষ করতে হলে সকাল পর্যন্ত খেতেই হবে, ঘুমটুম বাদ দিয়ে।’
জাহাঙ্গীর বলিল, ‘আচ্ছা, আরম্ভ তো করা যাক, তার পর তোমার কপাল আর আমার হাতযশ!’
খাওয়া শেষ হইলে জাহাঙ্গীর একা প্লাটফর্মে অন্যমনস্কভাবে পদচারণা করিতে লাগিল। হারুণ জাহাঙ্গীরের এই অন্যমনস্কতায় বিস্মিতও হইল না, ব্যাঘাতও জন্মাইল না। অনেককেই সে বলিতে শুনিয়াছে, জাহাঙ্গীরের মাথায় ছিট আছে। সে ইহা বিশ্বাস করে নাই। জাহাঙ্গীরের সঙ্গে বন্ধুত্ব তাহার যথেষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তাহাকে সে আপনার চোখ ও মন দিয়া যতটুকু দেখিয়াছে, তাহার অধিক জানিবার মতো অতি-কৌতূহল তাহার কোনোদিনই জাগে নাই। তাহার স্বভাবই এই। তাহা ছাড়া সে ইহাও মনে করে যে, যে স্বেচ্ছায় যতটুকু পরিচয় দেয়, তাহার অধিক জানিতে চেষ্টা করা খুব সুমার্জিত রুচির পরিচয় নয়। সে বলিত, কৌতূহল জিনিসটাই কদাকার। যাহা কেহ নিজে বলিতে চাহে না, তাহার উপর জুলুম করা বর্বরতারই কাছাকাছি। জাহাঙ্গীরকে যখন আর সকলে পাগল মনে করিত, তখন কেবল হারুণই ইহার পাগলামির, ইহার ছন্নছাড়া জীবনের মূলে কোনো সুগভীর বেদনা-উৎসের সন্ধান করিত। মানুষের বেদনাকে সে অশ্রদ্ধা করিতে শিখে নাই। তাই জাহাঙ্গীরের বেদনার উৎস-মূল জোর করিয়া খুঁড়িয়া বাহির করিতে চাহে নাই।
জাহাঙ্গীরের ইতিহাস সে তো জানেই না, অন্য ছাত্ররাও জানে না! জাহাঙ্গীরের পিতার মৃত্যুর পর যখন তাহার পিসতুতো ভায়েরা সম্পত্তি দাবি করিয়া নালিশ করিল, তখন তাহার বুদ্ধিমতী জননী এ কেলেঙ্কারি বেশি দূর পড়াইবার পূর্বে কী করিয়া যে ইহা চাপা দিয়া ফেলিল, তাহা দুই চারিজন ছাড়া কেহই জানিতে পারিল না। অবশ্য, ইহার জন্য তাহাদের বিপুল জমিদারির প্রায় এক চতুর্থাংশ আয় কমিয়া গেল। তাহার পিসতুতো ভায়েদের অবস্থা অত বড়ো মামলা চালাইবার মতো স্বচ্ছল ছিল না। জাহাঙ্গীরের মনও ধূমে বিষাক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু একেবারে দগ্ধীভূত হইল না। এই সান্ত্বনাটুকুই তাহার জীবনে বড়ো সম্বল হইয়া রহিল। এতদিন হয়তো সে সত্যই পাগল হইয়া যাইত, অথবা আত্মহত্যা করিত, শুধু স্বদেশ উদ্ধারের মন্ত্রই তাহাকে বাঁচিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, তাহার দগ্ধ জীবনকে প্রদীপ-শিখা করিয়া ঊর্ধ্বেতুলিয়া ধরিয়াছে। মরিতেই যদি হয়, জন্মের মতো অপরাধকে জীবনের জ্যোতিতে জ্যোতির্মহিমান্বিত করিয়া সে মরিবে।
কাজেই তাহারা এত সহজে অভাবনীয় রূপে যে সম্পত্তি পাইল, তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের সমস্ত দাবি পরিত্যাগ করিল, এমনকী, তাহারা আদালতে স্বীকারও করিল যে, জাহাঙ্গীর সত্যসত্যই খানবাহাদুরের বিবাহিত পত্নীর পুত্র। ইহা লইয়া ‘রায়-বাঘিনী’ জমিদারনির প্রতাপে জমিদারিতে কানাঘুষাও হইতে পারিল না। কাজেই এ ব্যাপার অনেকের মনে মনে ধোঁয়াইলেও আগুন হইয়া দেখা দিল না।
জাহাঙ্গীর যখন তন্ময় হইয়া পায়চারি করিতেছিল, তখন হারুণ আস্তে আস্তে উঠিয়া স্টেশন হইতে শহরে বেড়াইতে গেল। এই বেদনাতুর জাহাঙ্গীরকে সে যেন সহ্য করিতে পারিত না। তাহার এই মূর্তি সে যখনই দেখিয়াছে, তখনই তাহার বুক ব্যথায় মোচড় খাইয়া উঠিয়াছে। আজও সে সহিতে না পারিয়াই সরিয়া গেল। জাহাঙ্গীরের সম্মুখ দিয়াই সে চলিয়া গেল, কিন্তু জাহাঙ্গীর একটি কথাও বলিল না। এমনকি, তাহাকে দেখিয়াছে বলিয়াও মনে হইল না। কোন আবর্তে পড়িয়া সে তখন হাবুডুবু খাইতেছি, তাহা তাহার অন্তর্যামী ছাড়া কেহ জানিল না।
অন্যমনস্কভাবে পথ চলিতে চলিতে হারুণ যখন শহরে আসিয়া পড়িল, তখনও সমস্ত দোকানপাট বন্ধ হইয়া যায় নাই। সম্মুখে এক মনোহারীর দোকান দেখিয়া তাহার মনে পড়িয়া গেল, টাকার অভাবে সে তাহার ভাই বোনদের জন্য কলিকাতা হইতে তেমন কিছু আনিতে পারে নাই। জাহাঙ্গীর জোর করিয়া তাহাকে টিকিট কিনিতে দেয় নাই। রাস্তায়ও তাহার কোনো খরচ হয় নাই। ইহাতে তাহার যে চার পাঁচটি টাকা বাঁচিয়াছে, তাহা দিয়া সে তাহার ভাই-বোনদের জন্য সাবান, চিরুনি, ফিতা, গন্ধতেল প্রভৃতি কিনিল। ওই কয়টি টাকায় যাহা ক্রয় করিল, তাহা তাহার মনঃপুত হইল না। নিজের অসহায় অবস্থার কথা ভাবিয়া তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার মন খুশিতে ও বেদনায় ভরিয়া উঠিল, একটা কথা স্মরণ করিয়া। জাহাঙ্গীরের তোরঙ্গটা সে প্রথমে দেখে নাই, কিন্তু দেখা অবধি তাহার আর জানিতে বাকি নাই যে, জাহাঙ্গীর তাহার ভাই-বোনদের জন্যই কাপড়-চোপড় কিনিয়া লইয়া যাইতেছে।
অত খাবার যে সে একটু আগে লইয়া গিয়াছে – তাহার অর্থও সে বুঝিল। ইহাতে সে তাহাদের অভাবের সংসারে লালিত ভাই-বোনগুলির জন্য যেমন খুশি হইয়া উঠিল, তেমনই – বন্ধুর নিকট হইলেও – সেই আত্মীয়তাকে কিছুতেই প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারিল না। তাহার মন কেবলই বলিতে লাগিল, জাহাঙ্গীর এই পাগলামি করিয়া আমাদের দুর্দশার কথাটা স্মরণ না করাইয়া দিলেই ভালো হইত। ব্যথায় তাহার মন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল। বহুক্ষণ ধরিয়া উদ্দেশ্যবিহীনভাবে ঘুরিয়া ফিরিয়া সে যখন প্লাটফর্মে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখনও জাহাঙ্গীর তেমনই পায়চারি করিয়া ফিরিতেছে। সে কিছু না বলিয়া শুইয়া পড়িল। এই উন্মাদকে দেখিয়া তাহার মনের অনেকটা জ্বালা শান্ত হইয়া আসিল। ইহার বিরুদ্ধে তাহার মন যেটুকু অপ্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা তাহার কবি-মনের করুণ সহানুভূতির প্রীতিতে ধুইয়া মুছিয়া গেল।
আজ তাহার প্রথম মনে হইল, জাহাঙ্গীর শুধু তাহার চেয়ে দুঃখীই নয়, – তাহার চেয়েও সে দরিদ্র, সে সর্বহারা!
কুহেলিকা – ০৭
ভোর না হইতেই একটা দুরন্ত কোকিলের ডাকে হারুণের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সারারাত্রি সে নেশাখোরের মতো ঘুমাইয়াছে, পাশ পর্যন্ত ফিরে নাই। কত সুখের, কত বেদনার যেসব স্বপন সে সারারাত্রি ভরিয়া দেখিয়াছে, তাহার আবেশ যেন তখনও তাহার আঁখিপাতায় জড়াইয়া আছে।
উন্মত্ত যৌবনের অভূতপূর্ব সুখের পীড়ায় তাহার সারা দেহমন তখন চড়া সুরে বাঁধা বীণার মতো টনটন করিতেছিল। তাহার রক্তে রক্তে মহুয়া নেশার মতো কী যেন একটা পুলক রিনিরিনি করিয়া ফিরিতেছিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া সে তাহার কবিতার ডালি সাজায় সেই হাওয়া-পরিকে আজ সে চায় না, আজ এই কোকিলডাকা দক্ষিণা-বাতাসবহা গ্রীষ্ম প্রভাতে সে চায় সেই মাটির মানবীকে – যাহার মধ্যে তাহার সমস্ত কবিতা নিঃশেষ হইয়া যাইবে।…
হঠাৎ তাহার স্বপ্ন টুটিয়া গেল। জাহাঙ্গীর তখনও সামনে পায়চারি করিয়া ফিরিতেছে! সে জাহাঙ্গীরের নিকটে গিয়া দেখিল, তাহার দুই চক্ষু জবাসংকাশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, নিশিশেষের পাণ্ডুর গ্যাসের আলো পড়িয়া তাহার মুখ ভীষণ করুণ দেখাইতেছিল। অত্যন্ত প্রিয়জনকে স্বহস্তে হত্যা করিবার পর হত্যাকারীর মুখচোখ যেমন হয় তেমনি।
হারুণের কবি-মন হেরেমের কিশোরীর মতো, বন-মৃগীর মতো ভীরু, স্পর্শালু। কঠিন রূঢ় কোনো কিছুর স্পর্শ সে সহিতে পারে না; মারামারি তো দূরের কথা, কোথাও কলহ দেখিলেও সে থরথর করিয়া কাঁপিতে থাকে, তার সকল দেহমন বিস্বাদ ভয় ও হতাশায় একেবারে এলাইয়া পড়ে! সে সকল অন্তর দিয়া প্রার্থনা করে, জিজ্ঞাসা করি বিধাতাকে, কেন এই কলহ, কেন এই কুৎসিত সংগ্রাম, কেন এই অশান্তি! কবে মানুষ, মানুষ হইবে! খোদা, ইহাদের শান্তি দাও! ইহারা তোমার সুন্দর সৃষ্টিকে ভয়াবহ করিয়া তুলিল! তোমার ধরণির পুষ্পকুঞ্জ মত্ত রাবণের মতো ইহারা ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল।…
আজও সে জাহাঙ্গীরের এই ভীষণ মূর্তি দেখিয়া ভীত শুষ্ককণ্ঠে কোনোরকমে শুধু বলিতে পারিল, ‘জাহাঙ্গীর!’ সে আর কিছু বলিতে পারিল না। সমস্ত শরীর অজানা শঙ্কায় বেতসপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিল। জাহাঙ্গীর চমকিয়া উঠিয়া বলিল, ‘একী! হারুণ?’ বলিয়াই চারদিকে চাহিয়া লইয়া সলজ্জ অপ্রতিভ স্বরে বলিল, ‘ভোর হয়ে গেছে বুঝি? খুব ভয় পেয়ে গেছ তুমি, না? ও কিছু নয়, অমন আমার প্রায়ই হয়!’
হারুণ অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিল, ‘তুমি সারা রাত জেগে পায়চারি করেছ? আর আমি ষাঁড়ের মতন পড়ে পড়ে আরাম করে ঘুমিয়েছি?’
জাহাঙ্গীর বাম করে হারুণের কণ্ঠ মালার মতো জড়াইয়া ধরিয়া শান্তস্বরে বলিল, ‘তাতে হয়েছে কী ভাই! চলো আমরা বেরিয়ে পড়ি এই সময়। বেশ ঠান্ডায় ঠান্ডায় যাওয়া যাবে। কেমন? তুমি সব গুছোও, আমি স্টেশনের যে দুটো কুলিকে ঠিক করে রেখেছি আমাদের এই বোঁচকা-পুটুলি নিয়ে যাবার জন্যে, ওদের খুঁজে বের করি ততক্ষণ।’
জাহাঙ্গীর চলিয়া গেল। হারুণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো বিছানাপত্র গুছাইতে গুছাইতে ভাবিতে লাগিল জাহাঙ্গীরের এই অপূর্ব আত্মসংযমের মাধুর্য। হত্যাকারীর মতো ভীষণ রুক্ষ মুখ কেমন করিয়া চক্ষের পলকে এমন সুন্দর সহজ হাসিতে ভরিয়া উঠিতে পারে, তাহা সে কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিল না। সহসা তাহার মনে হইল, এই বেদনার এই দুঃখের বন্ধু জাহাঙ্গীর কাহাকেও করিতে চায় না – যত বড়ো অন্তরঙ্গ বন্ধু হোক সে, তাহাকেও জাহাঙ্গীর তার গোপন বেদনা-মন্দিরের সন্ধান বলিবে না। এইখানে সে একা – একেবারে একা! অমা-নিশীথিনীর অন্ধকারও সে রহস্যের সে বেদনার অন্ধকার পথে পথ না পাইয়া ফিরিয়া আসিবে!…
জাহাঙ্গীর যে এমন মিলিটারি-স্টাইলে এত জোরে – এতটা পথ হাঁটিয়া আসিতে পারিবে, হারুণ তাহা মনে করে নাই। কাজেই সারাটা রাস্তা জাহাঙ্গীরের সাথে প্রায় দৌড়াইয়া সে যখন তাহার স্বগ্রামের প্রান্তে আসিয়া পঁহুছিল, তখন আর থাকিতে না পারিয়া সে বলিল, ‘দোহাই ভাই, এই গাছতলায় একটু জিরিয়ে নিতে দাও! আর পারছিনে! বাপ! তুমি এতদিন ডাকহরকরা হওনি কেন? হাঁটা তো নয়, এ যেন হন্টন-প্রতিযোগিতার দৌড়!’ হারুণ বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে লাগিল।
জাহাঙ্গীর একেবারে শুইয়া পড়িয়া ঊর্ধ্বনেত্রে গাছের দিকে চাহিয়া বলিল, ‘কী সুন্দর ভাই তোমাদের এই দেশ! পূর্ববঙ্গের মতো একেবারে নিরবকাশ। গাছপালার ভিড় নেই। খানিকটা মাঠ, খানিকটা তেপান্তরের মতো শূন্য ডাঙা, খানিকটা বন জঙ্গল, দূরে দূরে গ্রাম, ক্ষীণাঙ্গী নদী – আমার কী ভালোই লাগছে, তা বলতে পারছিনে। কলকাতার ইটের পাঁজা থেকে বেরিয়ে গায়ে যেন একটু সুন্দর পবিত্র বাতাস লাগল। এমনই একটি ছোটো গাঁয়ে তোমার ওই বক্কেশ্বর নদীর ধারে যদি আমার একটি কুটির থাকত, তাহলে সারাদিন ওই ছেলেগুলোর সাথে গোরু চরিয়েই কাটিয়ে দিতে পারতাম।’
তাহার জন্মভূমির এই প্রশংসায় হারুণের বুক গর্বে খুশিতে ভরিয়া উঠিল। তাহার চক্ষু অকারণে জলে পুরিয়া উঠিল। সেই অশ্রু-পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা-আর্দ্র দৃষ্টি লইয়া হারুণ তাহার পল্লিজননীর পানে চাহিয়া রহিল। গণ্ড বাহিয়া দুই বিন্দু অশ্রুজলও বুঝিবা গড়াইয়া পড়িল। তাহার মনে হইতে লাগিল, তাহার এই গাঁয়ের পথের মাটি দুই হাতের অঞ্জলি পুরিয়া মাথায় মুখে মাখিয়া পবিত্র হইয়া লয়! লজ্জায় তাহা পারিল না, পার্শ্বেই জাহাঙ্গীর শুইয়া। সে অপ্রতিভ হইয়া বলিল, ‘জাহাঙ্গীর! সামনের পুকুরটাতে পা হাত ধুয়ে নাওনা ভাই! তোমার যে বুক পর্যন্ত ধুলো উঠেছে দেখছি! সুন্দর দেখাচ্ছে কিন্তু তোমায় এই ধুলোর গেরুয়া রঙে রাঙা হয়ে। তুমি যেন ঘরছাড়া বাউল!’ মুগ্ধদৃষ্টি দিয়া সে জাহাঙ্গীরের উচ্ছৃঙ্খল কেশ-বেশ দেখিতে লাগিল!
পুকুরপাড়ের একটা অর্জুন গাছের ডালে যে সুন্দর নীল পাখিটা বসিয়াছিল, জাহাঙ্গীর তাহারই দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়াছিল। এত সুন্দর পাখি সে আর কখনও দেখে নাই। সে উঠিয়া বসিয়া বলিল, ‘না হারুণ তোমাদের দেশে মাসখানেক থাকলে আমি একেবারে কবি বনে যাব! এত দেশ থাকতে কেন তোমাদেরই দেশে জয়দেব-চণ্ডীদাস জন্ম নেন, তা অনেকটা বুঝছি।’
সে আবার শুইয়া পড়িয়া বলিল, ‘না ভাই। এ ধুলো আর ধুচ্ছিনে পথে। বাংলার পথের ধুলো, আমার জন্মভূমির বেদনাতুর পথিকের পায়ের ধুলো – ও শুধু বুক পর্যন্ত কেন মাথা পর্যন্ত উঠলে আমি ধন্য হয়ে যেতাম! পবিত্র ধুলো কি এত তাড়াতাড়ি মুছতে আছে ভাই?’
বলিয়াই দিগন্তপ্রসারী মাঠের দিকে তাকাইয়া বলিল, ‘দেখো কবি, আমি কবিতা-টবিতা ভালো বুঝিনে! গোঁয়ার-গোবিন্দ লোক আমি। কিন্তু আমার আজ এই মাঠের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে, এর চেয়ে ভালো কবিতা তোমাদের কোনো কবিই লিখে যেতে পারেননি। এই মাঠের আলোর ছন্দোবদ্ধ লাইনের বন্ধনে কখনও সবুজ কখনও সোনার রঙে যে কবিতা লেখা হয়, তার কি তুলনা আছে! ওই কৃষকের লাঙলের চেয়ে কি তোমাদের কালিভরা লেখনী বেশি ফুলের ফসল ফলাতে পারে? ওই মাঠের খাতায় নিরক্ষর কবির সৃষ্টির কাছে তোমাদের জগতের সবচেয়ে বড়ো কবি কি তাঁর পুথির বোঝা নিয়ে দাঁড়াতে পারেন?
হারুণ দুই চক্ষে বিস্ময় ভরিয়া জাহাঙ্গীরের দিকে চাহিয়া রহিল। এই কি সেই কঠোর বাস্তবব্রতী বস্তুবিশ্বের পূজারি জাহাঙ্গীর? কিন্তু ইহা লইয়া সে প্রশ্নও করিল না। উহাকে সে কোনো দিনই বুঝিতে পারে নাই, আজও পারিল না। সে অন্যমনস্কভাবে বলিল, সত্যি ভাই, এরাই সত্যিকার ফুলের কবি, আমরা কথার কবি। আমরা যখন ঘরের আঁধার কোণে বসে মাকড়সার মতো কথার ঊর্ণা বুনি এরা তখন সারা দেশকে ফুলের ফসলের মতো সুন্দর রঙিন করে তোলে! এদের শ্রমেই তো ধরণির এত ঐশ্বর্য-সম্ভার, এত রূপ, এত যৌবন!’
জাহাঙ্গীর বলিল, ‘তাই ভাবছি হারুণ, এত বিপুল শক্তি এত বিরাট প্রাণ নিয়েও এরা পড়ে আছে কোথায়। এরা যেন উদাসীন আত্মভোলার দল, সকলের জন্য সুখ সৃষ্টি করে নিজে ভাসে দুঃখের অথই পাথারে। এরা শুধু কবি নয় হারুণ, এরা মানুষ! এরা সর্বত্যাগী তপস্বী দরবেশ! এরা নমস্য।’
জাহাঙ্গীর দুই হাত তুলিয়া সসম্ভ্রমে মস্তকে ঠেকাইল। হারুণের চোখ শ্রদ্ধায় বেদনায় বাষ্পাতুর হইয়া উঠিল। এই কি সেই প্রভাতের হত্যাকারীর মতো ভয়াবহ জাহাঙ্গীর!
কুলি দুইজন এইবার উঠিবার জন্য তাড়া দিতে লাগিল। জাহাঙ্গীর উঠিয়া কুলির মাথা হইতে হারুণের বোঁচকা ও নিজের বেতের বাক্সটা হাতে লইয়া বলিল, ‘চল’। হারুণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া জাহাঙ্গীরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।
জাহাঙ্গীর ঈষৎ হাসিয়া বলিল, ‘অন্যায় করেছি বন্ধু এক জন মানুষের বোঝা আমারই মতো আরেক জন মানুষের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে। কিন্তু আমরা এসে পড়েছি। অর্থ দিয়ে কি মানুষের হাতের সেবার, তার শ্রমের প্রতিদান দেওয়া যায়? এখন এই রাস্তাটুকু ওদের সুদ্ধ কাঁধে করে বয়ে নিয়ে গেলেও এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না।… মানুষের একটা নূতন বেদনার দিক দেখতে পেলাম আজ। এতদিন বইয়ের পাতায় যাকে দেখেছি, আজ চোখের পাতায় তার দেখা পেলাম।…’
হারুণ কিছুই বুঝিতে পারিল না। জাহাঙ্গীরের তাহার সাথে আসা হইতে আরম্ভ করিয়া এই রাস্তায় চলা পর্যন্ত যেসব ব্যাপার সে দেখিল, যাহা কিছু শুনিল, তাহাতে তাহার মধ্যে তাহার সমস্ত চিন্তা সমস্ত কিছু যেন একটা তাল পাকাইয়া গিয়াছে। সে নিঃশব্দে অভিভূতের মতো পথ চলিতে লাগিল।
গ্রামে প্রবেশ করিয়া দুই একটি বাড়ি পরেই তাহাদের জীর্ণ খোড়ো ঘর। হারুণ ঘরের দুয়ারে আসিয়া পঁহুছিতেই তাহার দুইটি বোন ছুটিয়া আসিয়া তাহার পায়ের ধুলা লইল। তাহারা তাহাদের আনন্দের আতিশয্যে হারুণের পিছনে জাহাঙ্গীরকে দেখিতে পায় নাই। হঠাৎ তাহার দিকে চোখ পড়িতেই তাহারা জিভ কাটিয়া ছুটিয়া পলাইল।
হারুণ বাহিরের ঘরের দরজা খুলিয়া দিয়া ভাঙা তক্তপোশে বিছানা পাতিয়া দিবার উদ্যোগ করিতেই জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, ‘দোহাই হারুণ, তোমার ভদ্রতা রাখো! তুমি নিরতিশয় অতিথিপরায়ণ, মেনে নিলাম। তুমি আগে তোমার বাবা-মা ভাই-বোনের সাথে দেখাশুনা করে এসো।’
হারুণ হাসিয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল। এমন সময় তাহার মা আলুথালুবেশে চিৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকিয়া বলিতে লাগিলেন, ‘খোকা এসেছিস? খোকা এসেছিস? আমার জন্যে পালকি এনেছিস ? মিনার জন্য সাইকেল এনেছিস? মিনা যাবে সাইকেলে, আমি যাব পালকিতে – হুই গোরস্থানে! মিনার সাইকেল! মিনা!’ বলিয়াই আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।
হারুণের জননী উন্মাদিনী। হারুণের আর একটি ভাই ছিল, হারুণের চেয়ে দু-বছরের বড়ো, ডাক নাম ছিল তার – মিনা। তেরো বৎসর বয়সে সে মারা যায়। তাহার পরেই তাহার মাতা পাগল হইয়া যান। তাহার পিতারও কিছুদিন আগে বসন্ত হয়, তিনি কোনোরকমে বাঁচিয়া যান, কিন্তু দুইটি চক্ষু চিরজন্মের মতো অন্ধ হইয়া যায়।
মৃত্যুর সময় মিনা বিকারগ্রস্ত অবস্থায় কেবলই কাঁদিয়াছিল, ‘আমি সাইকেল চড়ব, আমায় সাইকেল কিনে দাও!’ দুর্ভাগিনি মাতা পাগল হইয়া গেলেও ‘মিনা’ আর ‘সাইকেল’ এই দুটি কথা ভুলিতে পারেন নাই।
হারুণের দুইটি বোন ও ছোটো ভাইটির এই পাগলিনি মাতা ও অন্ধ পিতাকে লইয়া যে কী করিয়া দিন কাটে, তাহা ভাবিয়া জাহাঙ্গীরের শরীরের রক্ত হিম হইয়া যাইতে লাগিল। অথচ হারুণ একদিনও তাহার এই অসহায় অবস্থার কথা তাহার কাছে বলে নাই।
হারুণ তাহার মাতাকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িল। জাহাঙ্গীর আর থাকিতে না পারিয়া আগাইয়া আসিয়া পায়ের ধুলা লইয়া বলিল, ‘মা ভিতরে চলুন!’
মাতা তাহার দিকে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল চোখে চাহিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, ‘মিনা এসেছিস? অ্যাঁ? তোর সাইকেল কই? আমার পালকি কই?’
হারুণ ও জাহাঙ্গীর ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে ঘরে আনিয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল। জাহাঙ্গীর চলিয়া আসিতেছিল, কিন্তু মাতা ডুকরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, ‘মিনা চলে গেলি? ও খোকা? মিনাকে ধর ধর! পালাল পালাল!’
জাহাঙ্গীর চলিয়া আসিতেছিল দেখিয়া হারুণের দুই বোন আসিয়া মাতাকে ধরিয়াছিল, কিন্তু মায়ের এই ক্রন্দনে জাহাঙ্গীর ফিরিয়া আসিতেই তাহারা আবার উঠিয়া পলাইল। হারুণ একটু রাগিয়া বলিয়া উঠিল, ‘এ-সময় অত বিবি হতে হবে না তোদের! এ আমার বন্ধু জাহাঙ্গীর। আমাকে দেখে যদি লজ্জা না করিস তো জাহাঙ্গীরকেও লজ্জা করবার কিছু নেই।’
এইবার তাহারা কোনোরকমে জড়সড় হইয়া মায়ের কাছে আসিয়া বসিল। হারুণ কী ইঙ্গিত করিতেই তাহারা দুই বোন জাহাঙ্গীরের পায়ে হাত দিয়া সালাম করিল। জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, ‘কী দোওয়া করব? রাজরানি হও না অন্য কিছু?’ বলিয়াই দেখিল ঘোমটার আড়াল হইতে এক জোড়া উজ্জ্বল সুন্দর চক্ষু ভোরের তারার মতো তাহার দিকে চাহিয়া আছে। জাহাঙ্গীরের বুক কাঁপিয়া উঠিল, সে চোখ ফিরাইয়া লইল! মাতা তখন অনেকটা শান্ত হইয়াছেন। জাহাঙ্গীরের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে তিনি মাঝে মাঝে অস্ফুটস্বরে বলিতেছিলেন, ‘মিনা! বাবা আমার! তুই আর যাসনে। আমি সাইকেল কিনে দেব!’
কুহেলিকা – ০৮
পরদিন অসহ্য গরমে অতি প্রত্যুষেই জাহাঙ্গীরের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে উঠিয়াই বাহিরবাটী হইতে হারুণকে চিৎকার করিয়া ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল। হারুণ ঘুম-বিজড়িত চক্ষে উঠিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘কী হয়েছে জাহাঙ্গীর? কিছু হয়েছে নাকি?’
জাহাঙ্গীর বলিল, ‘আরে তৌবা, তোমাদের দেশটা দেখছি জ্যৈষ্ঠি বুড়ির একেবারে উনোনের পাশ! কাল রাত্তির থেকে সকাল পর্যন্ত আমার অন্তত তিন কলসি ঘাম ঝরেছে! বাপ!’
হারুণ হাসিয়া ভালো করিয়া কাছাটা গুঁজিতে গুঁজিতে বলিল, ‘আমি তো সেই জন্যেই কাল ভিতরে গিয়ে শুতে চাইনি। তোমার কাছে থাকলে অন্তত খানিকক্ষণ পাখা করতে পারতাম।’ বলিতে বলিতে আবার বসিয়া পড়িল!
জাহাঙ্গীর হাসিয়া উঠিল। প্রভাতের আকাশের মতো খোলা প্রাণের হাসি, সুন্দর উজ্জ্বল! বলিল, ‘বন্ধু তোমার ব্যাক-টাইটা আগে ভালো করে এঁটে নাও গিয়ে! আমি বরং ততক্ষণ একটু সাঁতার কাটি তোমাদের ওই এঁদো পুকুরটাতে!’ – বলিয়াই জাহাঙ্গীর তাহার বেতের বাক্সটা খুলিয়া চায়ের সরঞ্জাম বাহির করিয়া স্টোভটা জ্বালাইয়া চায়ের জল চড়াইয়া দিয়া তোয়ালে সাবান লইয়া পুকুরে ঝাঁপাইয়া পড়িল। হারুণ সস্মিত আননে তাহার সাঁতার-কাটা দেখিতে লাগিল।
সাঁতার কাটিতে কাটিতে জাহাঙ্গীর বলিল, ‘হারুণ, পানিটা গরম হয়ে গেলে তোমার বোনকে নিয়ে একটু চা-টা তৈরি করে নিয়ো ভাই। চা দুধ চিনি সব ওই বাক্সে আছে। দোহাই তুমি তৈরি করতে যেয়ো না যেন! সব ভণ্ডুল করবে তা হলে!’ – বলিয়াই জাহাঙ্গীর এক ডুবে মাঝপুকুর হইতে ঘাটে আসিয়া চুলগুলো পিছন দিকে সরাইয়া বলিয়া উঠিল, ‘হারুণ, তখন বলছিলে, রাত্রে আমার কাছে থাকলে খানিকক্ষণ পাখা করতে পারতে, না? তা হলে যেটুকু ঘুম আমার হয়েছিল, তা-ও হত না! বাপ! পাশে শুয়ে একটা মদ্দ মিনশে পাখা করছে দেখলে ঘুম বেচারি ঘোমটা টেনে তিন লাফে ঘর ছেড়ে পালাত। পুরুষের সেবা – উঃ সে কী ভয়ানক! ভাদ্দর বউকে ভাসুর সেবা করতে এলে তার যেমন অবস্থা হয়, তেমনই আর কী।’
হারুণ এইবার একটু জোরেই হাসিয়া ফেলিল। বলিল, ‘দোহাই ভাই, ওই দুঃখে তুমি জলে ডুবো না যেন! আমি কোনোদিনই তোমার সেবা করতে যাচ্ছিনে। চা-টা ভূণীকেই করতে বলছি। তবে সেও আমার চেয়ে বেশি অভিজ্ঞ নয়।’
তাহার কথার অর্থ অনুরূপ দাঁড়াইল দেখিয়া জাহাঙ্গীর একটু লজ্জিত হইয়া উঠিল। তবে সে তুখোড় ছেলে, সহজে মুষড়াইয়া যায় না। বলিল, ‘তা হোক গে, মা খাবার না রেঁধে যদি বাবা ও কর্মটা করতেন, তা হলে এর অনেকটা স্বাদ কমে যেত হে!’ বলিয়াই জাহাঙ্গীর আবার সাঁতার কাটিতে আরম্ভ করিল।
হারুণ বাড়িতে গেয়ে তাহার বোন ‘ভূণী’কে হাসিতে হাসিতে বলিল, ‘ওরে ভূণী, জাহাঙ্গীর স্টোভে চা চড়িয়ে নাইতে গেছে। তুই চা-টা একটু তৈরি করে রাখ গিয়ে। চা, দুধ, চিনি, কাপ, চামচ সব ওইখানেই আছে। ওর ওই একটা দোষ, কোথাও যাবার সময় চায়ের সরঞ্জাম সাথে না নিয়ে যায় না।’
ভূণী হারুণের বোন দুটির মধ্যে বড়ো। বয়স পনেরো পার হইয়া গিয়াছে। দেখিতে কিন্তু আরও একটু বেশি বয়সের বলিয়াই মনে হয়। চমৎকার জ্বলজ্বলে চোখমুখ। সমস্ত শরীরে বুদ্ধির প্রখর দীপ্ত জ্যোতি যেন ঠিকরিয়া পড়িতেছে। সে তাহার ভ্রাতার আদেশে বাহিরবাটীতে যাইতে একটু ইতস্তত করিল। ওর ঘর হইতে পুকুরটা একেবারে সামনে। তাছাড়া সে ভালো চা করিতেও জানে না। বাড়িতে ও পাট একেবারেই নাই।
হারুণ বুঝিতে পারিয়াই একটু দুষ্টুমি করিয়া বলিল, ‘ওরে ভূণী, জাহাঙ্গীর বলেছে, তুই – এই তোরা কেউ চা তৈরি করে না দিলে ও কিছুতেই খাবে না। পুরুষ লোকের সেবা আর রান্না জিনিসের উপর ওর ভয়ানক আক্রোশ! আমি চা করলে ও হয়তো তা আমার মুণ্ডুতেই ঢেলে দেবে।’
ভূণী যাইতেছিল, আর তাহার যাওয়া হইল না। সে লজ্জার রাঙা হইয়া বলিল, ‘আমি যেতে পারব না, মোমিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।’
ভূণীর ছোটো বোন মোমি আজও দ্বাদশীর চাঁদ। ভূণীর মতো আজও সে ষোলো কলায় পূর্ণ হইয়া ওঠে নাই। সে কাছেই দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিল এবং তাহার চোখে-মুখে দুষ্টুমির হাসি দেখিয়া বেশ বোঝা যাইতেছিল যে, সে এই ব্যাপারের রহস্যটুকু রীতিমতো উপভোগ করিতেছে।
এ দেশের সম্ভ্রান্ত মুসলমান ঘরেও ‘দিদি’-কে পূর্ববঙ্গের মতো ‘আপা’ না বলিয়া ‘বুবু’ বলিয়াই ডাকে।
তাহার বুবুর কথা শুনিয়া মোমি ঝংকার দিয়া বলিয়া উঠিল, ‘ইস! আমি যেতে গেছি আর কী! তোমায় ডেকেছেন, তুমি যাও।’
ভূণী কোপ প্রকাশ করিয়া বলিল, ‘এই মোমি! যা তা বললে তোমার পিঠে চ্যালাকাঠ ভাঙব কিন্তু!’
হারুণ হাসিয়া বলিল, ‘নে আর ঝগড়া করতে হবে না। চল, আমরা তিন জনেই যাই। আমি বসে থাকব, তোরা চা করবি।
মোমি খুশি হইয়া উঠিল। ভূণী কিন্তু একটু সলাজ সংকোচেই গেল।
বাহির বাড়িতে যাইয়া ভূণী পুকুরের দিকে চাহিতেই জাহাঙ্গীরের সাথে চোখাচোখি হইয়া গেল। জাহাঙ্গীর চোখ নামাইয়া লইল। ভূণী কিন্তু ইচ্ছা করিয়াও চোখ নামাইতে পারিল না। রাত্রিবেলায় বনহরিণীর চোখে শিকারির ফ্লাশ-লাইটের জ্যোতিঃধারা গিয়া পড়িলে সে যেমন মুগ্ধবিস্ময়ে সেই আলো হইতে চোখ ফিরাইয়া লইতে পারে না, তেমনি করিয়া ভূণী জাহাঙ্গীরের অনাবৃত সুঠাম সুডৌল বলিষ্ঠ দেহের পানে চাহিয়া রহিল। ইচ্ছা করিয়াও চক্ষু ফিরাইতে পারিল না। ইহা যে লজ্জার, ইহা যে অন্যায়, ইহা সে ভাবিবার অবকাশ পর্যন্ত যেন পাইল না।
জাহাঙ্গীরের বিরাট বক্ষ স্নানের শ্রমে ঘন ঘন আন্দোলিত হইতেছিল, শরীরের সমস্ত মাংসপেশী পরিপূর্ণভাবে ফুলিয়া উঠিয়াছিল। সে এইবার ঘাটে পিছন ফিরিয়া বসিয়া সাবান মাখিতে মাখিতে স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিল, তাহার পৃষ্ঠে একজোড়া খরদৃষ্টির উষ্ণতা আসিয়া লাগিতেছে!
জাহাঙ্গীর এইখানে একটু লাজুক। সে মহিলাদের সঙ্গে অতিমাত্রায় মিশিতে পারে, মিশিতে চায়ও। কিন্তু কোনো মেয়ে একটু খরদৃষ্টিতে চাহিলে সে আর চোখ তুলিতে পারে না। মেয়েদের সে যেমন পছন্দ করে, তেমনই ভয়ও করে। অশ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয়।
সে একবার হাজারিবাগের জঙ্গলে শিকারে গিয়াছিল। একদিন রাত্রে সে ফ্লাশ-লাইট দিয়া শিকার খুঁজিতেছিল। হঠাৎ একটা হরিণের চোখে সেই লাইট পড়ায় হরিণ এমন করিয়া সুন্দর ভীতির চাহনি দিয়া তাহার দিকে চাহিয়াছিল, যে, সে আর তাহাকে গুলি করিতে পারে নাই। আজও ইচ্ছা করিয়াই পিছন ফিরিয়া ঘাটে বসিয়া সাবান মাখিতে লাগিল। যে হরিণী তাহার দিকে এখনই এমনি করিয়া তাকাইয়াছিল, জাহাঙ্গীর জানে, ইচ্ছা করিলেই তাহাকে হত্যা করিতে পারে, তবু সে বিরত হইল। তাহার কেমন যেন দয়া হয় উহাদের দেখিলেই! উহাদের চোখ জাদু জানে। উহাকে এড়াইয়া চলাই ভালো – জাদুকরিকে হত্যা করায় পৌরুষ নাই।
নারী – তাহাকে সে যেমন অশ্রদ্ধা করে তেমনই ভালোও বাসে – উহারা সুন্দর জাদুকরি।… জাহাঙ্গীরের রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠে, দেহের মাংসপেশীসমূহ প্রস্তরকঠিন হইয়া উঠে। একবার মনে করে, ওই সুন্দর চোখের সুন্দর জীবগুলোকে নির্মম হস্তে সে হত্যা করিতে পারে! উহাদের চোখ সুন্দর, উহাদের মন ছলনায় কুটিল!…
জাহাঙ্গীর যখন স্নান সারিয়া উঠিয়া আসিল, তখন চা হইয়া গিয়াছে।
ভূণী ভিতরে চলিয়া যাইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিল, সদ্যস্নাত জাহাঙ্গীর তাহার গ্রিক ভাস্করের নির্মিত মর্মরমূর্তির মতো অনাবৃত দেহ লইয়া দাঁড়াইয়া আছে।
আদিম মানব প্রথম অরুণোদয় দেখিয়া যেমন বিস্ময়ান্বিত চোখে জবাকুসুমসংকাশ তরুণ অরুণের পানে চাহিয়া দেখিয়াছিল, এ তেমনই দৃষ্টি।
জাহাঙ্গীর তাহাকে অপ্রতিভ হইবার অবসর না দিয়া বলিয়া উঠিল, ‘দাঁড়াও ভাই ভূণী, পালিয়ে যেয়ো না। চা-টা যখন তৈরিই করলে, তখন না খাইয়ে আর যেয়ো না। কেমন?’ বলিয়াই মোমির দিকে চাহিয়া বলিল, ‘তোমার এখনও লজ্জা হওয়ার মতো বয়স হয়নি, তুমি কেন অমন জড়-পুঁটুলি হয়ে বসে আছ ভাই?’
মোমি সত্যিই এতক্ষণ বিয়ের কনেটির মতো কাপড় ঢাকা দিয়া এক কোণে বসিয়াছিল, এইবার খুক খুক করিয়া হাসিতে লাগিল এবং একটু পরেই ঘোমটা খুলিয়া হাসিতে হাসিতে দৌড়িয়া ভিতরে চলিয়া গেল।
জাহাঙ্গীর কাপড় বদলাইয়া চৌকাঠটার উপর বসিয়া ভূণীর দিকে হাত বাড়াইয়া বলিল, ‘দাও ভাই, চা-টা দাও!’
ভূণীকে কে যেন মন্ত্র দিয়া বশ করিয়াছে।
মন্ত্রাহত সাপিনির মতো সে না পারিল পালাইতে, না পারিল ফণা তুলিতে।
সে আস্তে আস্তে এক কাপ চা হারুণকে দিয়া দ্বিতীয় কাপটা কাঁপিতে কাঁপিতে জাহাঙ্গীরের হাতে দিল। আর একটু হইলেই পেয়ালাটা পড়িয়া গিয়াছিল আর কী! জাহাঙ্গীর তাড়াতাড়ি পেয়ালাটা ধরিতে গিয়া ভূণীর কয়েকটা আঙুল ধরিয়া ফেলিল। লজ্জা ঢাকিবার জন্য তাড়াতাড়ি চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়া জাহাঙ্গীর চিৎকার করিয়া উঠিল, ‘বাঃ বাঃ কী চমৎকার চা-ই হয়েছে ভূণী!’
ভূণী ততক্ষণে লজ্জায় ঘামিয়া লাল হইয়া উঠিতেছিল। আর একটু থাকিলেই হয়তো সে মূর্ছিত হইয়া পড়িত। কিন্তু তাহাকে আর থাকিতে হইল না। তাহার অন্ধ পিতা উঠিয়া তাহাকে বাড়ির ভিতর হইতে ডাকাডাকি শুরু করিয়া দিলেন। সে তাড়াতাড়ি পালাইয়া বাঁচিল।
হারুণ এতক্ষণে কী যেন ভাবিতেছিল। তাহার আদরের বোনের এই ভাবান্তর সে লক্ষ করিয়াছিল। ইহা লইয়া সে আপন মনে কত কী আকাশ-কুসুমের সৃষ্টি করিতেছিল। কত সুখের স্বপন, কত ভবিষ্যতের রাঙা উৎসবের রাঙা দিন, আরও কত কী!
জাহাঙ্গীর চা খাইতে খাইতে বলিল, ‘ছেলেমানুষ এরা, নাস্তা তৈরি করতে দেরি হবে হারুণ, এসো দুটো বিস্কুট খাই।’ হারুণ আপত্তি করিল না। অন্যমনস্কভাবে বিস্কুট ও চা খাইতে লাগিল।
জাহাঙ্গীর হঠাৎ চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, ‘এই মোমি! মোমি! আমার চায়ের কাপটা শেষ হয়ে গেছে। তুমি এসে না দিলে আর এক কাপ চা কিছুতেই খাচ্ছিনে!’
মোমি বেড়ার পাশেই উঁকি মারিতেছিল। একটু বাঁকিয়া বাঁকিয়া কাছে আসিয়া চায়ের কাপটা জাহাঙ্গীরের হাতে দিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেই জাহাঙ্গীর খপ্ করিয়া তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, ‘আমার সঙ্গে চা না খেলে আমি কিচ্ছু খাব না কিন্তু!’
হারুণ হাসিয়া বলিল, ‘খা না, এও তোর দাদাভাই!’ জাহাঙ্গীরকে বলিল, ‘ওকে তুমি চেন না জাহাঙ্গীর, ভয়ানক দুষ্টু। একটু আলাপ জমে গেলে তোমায় নাকাল করে ছাড়বে। কোনোদিন রাতে হয়তো তোমার কাছায় বেড়াল-বাচ্চা বেঁধে দেবে। ওর দুষ্টুমির জ্বালায় বাড়ির সকলে অস্থির!’
জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, ‘সত্যি! তবে রে দুষ্টু, কিছুতেই চা না খাইয়ে ছাড়ছি না তা হলে!’….
একটু পরেই দেখা গেল, মোমি কলিকাতা সম্বন্ধে তাহার অদ্ভুত অদ্ভুত ধারণা লইয়া প্রশ্ন করিয়া জাহাঙ্গীরকে চা খাইবার অবসর পর্যন্ত দিতেছে না।
জাহাঙ্গীরও অকুতোভয়ে বলিয়া যাইতেছিল, ‘কলকাতার লোকগুলোর দাড়ি হয় না, সেখানে কাপড় ময়লা হয় না, চুলের তেড়ি ভাঙে না। সেখানে মানুষ পায়ে হাঁটে না, তারা কোমর পর্যন্ত মানুষ, তার পর চারটে চাকা। তাদের চারটে চারটে চোখ। পুরুষের গোঁফ দাড়ি হয় না। মেয়েরা ছেলেদের মতো করে চুল কাটে; ছেলেরা মেয়েদের মতো চুল বড়ো রাখে। পুরুষে রান্না করে, মেয়েরা থিয়েটার দেখে, নাচে। ছেলেরা বাঁদর হয়ে বাবাকে ভল্লুক করে তার পিঠে চড়ে শ্বশুরবাড়ি যায়, মেয়েরা ডুগডুগি বাজায়!’
এমন সময় হারুণের ছোটো ভাইটি তাহার অন্ধ পিতার হাত ধরিয়া বৈঠকখানায় লইয়া আসিল।
জাহাঙ্গীর তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহার পায়ে হাত দিয়া সালাম করিয়া বলিল, ‘কাল আর আপনার সাথে ভালো করে আলাপ করতে পারিনি। আমরা চা খাচ্ছি, একটু দেব? খাবেন?’
হারুণের পিতা খুশি হইয়া বলিলেন, ‘দাও বাবা, দেখি ভূণী কেমন চা করলে! ভূণী চা করতে পেরেছে তো? আমরা তো কেউ খাইনে। আমিও এক কালে প্রায় তোমার মতো চা-খোর ছিলাম বাবা।’ বলিয়াই গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কোনো সুখময় অতীতকে তাঁহার অন্ধ চক্ষু দিয়া যেন দেখিবার চেষ্টা করিলেন!
জাহাঙ্গীরের মন করুণায় ভিজিয়া উঠিল। মুখের চা বিস্বাদ হইয়া উঠিল।
চায়ের কাপে চুমুক দিয়াই হারুণের পিতা বলিয়া উঠিলেন, ‘সত্যিই, ভূণী চমৎকার চা করেছে তো রে! ভূণী! ও ভূণী!’
ভূণী সলজ্জভাবে দরজার পাশে আসিয়া অধোমুখে আঙুলে আঁচলের প্রান্ত লইয়া জড়াইতে লাগিল।
হারুণ বলিল, ‘ওই ভূণী এসেছে। কিছু বলছিলে তাকে?’
পিতা হঠাৎ কেমন যেন বিষাদের সুরে বলিলেন, ‘না, কিছু না। মোবারক কোথায় গেলি?’
মোবারক হারুণের ছোটো ভাই। ছেলেটি অদ্ভুত – শান্ত ধীর প্রকৃতির। এই বয়সেই যেন বিশ্বের বিষণ্ণতা আসিয়া তাহাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। মুখে চোখে আনন্দের এতটুকু ক্ষীণ রেখাটিও নাই। বর্ণ ফ্যাকাশে সাদা, লিকলিকে, পাঁজরের হাড় কটি গোনা যায়।
মোবারক চা খাইতেছিল। পিতার ডাকে চকিত হইয়া শান্তস্বরে বলিল, ‘এই যে চা খাচ্ছি!’
এরই মাঝে জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, ‘আমরা সকলে চা খাচ্ছি, ভূণী যদি না খাও তাহলে…’
জাহাঙ্গীর আর কিছু বলিবার আগেই হারুণের পিতা বলিয়া উঠিলেন, ‘আয় ভূণী, তোর মা তো এখনও ঘুমুচ্ছেন, তুইও খা না একটু! এমন সোনার ছেলের কাছে কি লজ্জা করতে আছে? মনে কর না, ও তোর মিনা ভাই!’ – বলিয়াই পিতা চায়ের কাপ মাটিতে রাখিয়া পাঁজরফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন!
ভূণী আর দ্বিরুক্তি না করিয়া নিজের হাতে চা করিয়া খাইতে খাইতে বলিল, ‘বাবা তুমি চা খাও, এই আমি খাচ্ছি।’
জাহাঙ্গীর দেখিল, ভূণীর দুই আয়ত চক্ষু জলে টইটুম্বর হইয়া উঠিয়াছে। সে আর এ দৃশ্য সহিতে পারিতেছিল না। হঠাৎ সে বলিয়া উঠিল, ‘মোমি এসো তো ভাই, আমরা ওই তোরঙ্গটা খুলি। ওতে কলকাতার বড়ো বড়ো বাঁদর আছে, দেখবে?’
মোমি চিৎকার করিয়া বলিল, ‘ওরে বাপরে! ও কামড়ে দেবে, আমি কুছুতেই খুলতে পারব না!’
জাহাঙ্গীর হাসিয়া নিজের তোরঙ্গটা খুলিয়া একরাশ কাপড়জামা বাহির করিয়া হারুণের পিতাকে বলিল, ‘আমি এদের জন্য কিছু কাপড়জামা এনেছি, আপনি আদেশ না দিলে ওরা হয়তো নেবে না। ওরা তো আমারও ভাই-বোন!’ একটু থামিয়া আবার বলিল, আমার একটিও ছোটো ভাইবোন নেই বলে আমার এত দুঃখ হয়। তাই বন্ধুদের ভাইবোন নিয়ে সে সাধ মেটাই। ভাই মোমি, এসব নেবে তো ? না নিলে কিন্তু আজই চলে যাব আমি।’
হারুণ একটু উচ্চকণ্ঠেই বলিয়া উঠিল, ‘এসব আবার করেছ কী? এসব দামি কাপড় কিনতে তোমার তিন চারশো টাকার কম পড়েনি যে! এসব কখন করলে বলো তো! মিষ্টি সন্দেশ তো এনেছ বাগবাজার আর শিউড়ি উজাড় করে!’
জাহাঙ্গীর হাসিয়া একটু নিম্নকণ্ঠে বলিল, ‘এই স্টুপিড, তুমি চুপ করো। সরকার কা মাল, দরিয়া মে ডাল! জমিদারির এত টাকা নিয়ে কী করব? পাপের ধন পরাচিত্তিতে যাক! আমার ভাইবোন থাকলে খরচ করতাম না?’
হারুণের পিতা অত্যধিক খুশি হইয়া একটু ভারীকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, ‘এর পরে আর কী বলব বাবা! খোদা তোমাকে সহি-সালামতে রাখুন, হায়াতদারাজ করুন! তুমি সত্যই আমার ছেলের চেয়ে বড়ো। যে দানে অহংকার নেই, তাকে কি উপেক্ষা করতে আছে?’
ভূণী তাহার জলভরা বড়ো বড়ো দুইটি চোখ তুলিয়া জাহাঙ্গীরের দিকে তাকাইয়া থাকিল। সেই দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা করুণা স্নেহ যেন উছলিয়া পড়িতেছিল।
হারুণের পিতা হঠাৎ হাসিয়া বলিলেন, ‘ওরে ভূণী, মোমি, মোবারক! তোরা যা, নতুন কাপড় পরে দেখা, কেমন মানাল! আর সালাম কর জাহাঙ্গীরকে। নতুন কাপড় পরে যে সালাম করতে হয়।’
মোমি কাপড়ের রাশ লইয়া ভূণীকে হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া গেল। মোবারক উঠিল না। শান্তভাবে বসিয়া রহিল। কাপড় জামা পাইয়া সে খুশি না বিরক্ত হইয়াছে, কিছুই বোঝা গেল না।
জাহাঙ্গীর একটু আশ্চর্য হইয়া বলিল, ‘মোবারক, অমন করে বসে যে। তোমার বুঝি কাপড় পছন্দ হল না? আচ্ছা দেখো তোমার জন্য কী এনেছি।’
বলিয়াই একটা ফুটবল বাহির করিয়া বলিল, ‘এই নাও। আজ বিকেলে সকলে মিলে ফুটবল খেলা যাবে, কেমন?’
মোবারক তাহার আনত চক্ষু তুলিয়া বিষণ্ণ মলিন দৃষ্টিতে জাহাঙ্গীরের দিকে তাকাইয়া বলিল, ‘আমি তো ফুটবল খেলিনে। ও সময় বাবাকে নিয়ে একটু বেড়িয়ে আসি।’
জাহাঙ্গীরের মন দুঃখের ম্লানিমায় মলিন হইয়া উঠিল। সে কেমন যেন হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল। এত দুঃখের মাঝেও মানুষ বাঁচে কেমন করিয়া।
একটু আলাপ-সালাপ হইতেই মোমি তাহার সিল্কের জামাকাপড় পরিয়া আসিয়া জাহাঙ্গীরের পায়ে হাত দিয়া সালাম করিয়া বলিল, ‘তোমরা সকলে ভিতরে এসো, নাস্তা করবে।’
ভিতরবাটীতে যাইতে যাইতে হারুণ হাসিয়া বলিল, ‘গ্রিন রংটা তোকে বেড়ে মানিয়েছে তো রে মোমি! দেখেছ, মোমির আর্ট-জ্ঞান হয়েছে!’ বলিয়াই তাহার মাদ্রাজি ঢং-এ কাপড় পরিবার ধরনটার দিকে ইঙ্গিত করিল।
জাহাঙ্গীরও সে হাসিতে যোগ দিয়া বলিল, ‘সত্যই ওকে তো সুন্দর মানিয়েছে! কাপড় পরাটাও সুন্দর হয়েছে।’
মোমি জাহাঙ্গীরের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে যাইতে বলিল, ‘ও আল্লা! এ আমি বুঝি পরেছি? বুবু পরিয়ে দিয়েছে! বুবুকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে! দেখবেন চলুন!’
জাহাঙ্গীর তাড়া দিয়া বলিল, ‘আবার আপনি? “তুমি” বলবে। আর “দাদা ভাই” – কেমন?’
মোমি বড়ো বড়ো দু-চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিল, ‘ও মা! কী হবে! এক দিনেই নাকি একটা মিনসেকে তুমি বলা যায়!’ সকলে হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল। মোমি লজ্জা পাইয়া ছুটিয়া পলাইল।
ভিতরে গিয়া বসিতেই শোনা গেল, হারুণের মাতা জাগিয়া উঠিয়া ভূণীর সাজসজ্জা দেখিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, ‘ওরে মা, তুই শ্বশুরবাড়ি চলে গেলে আমি থাকব কী করে? আমার মিনার মতোই যে তোর চোখ মুখ। মা তুই শ্বশুরবাড়ি যাসনে! দামাদ মিয়াঁকে (জামাই) বল, সে ঘরজামাই থাকবে।’
জাহাঙ্গীর হাসিবে না কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না। হারুণ তাড়াতাড়ি ভিতরে গিয়া ভূণীকে বলিল , ‘ভূণী তুই বাইরে চলে আয় না!’ কিন্তু আর কিছু বলিবার আগেই ভূণীকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, ‘সত্যি ভূণী, এতে আর দোষ কী! আমিই যে চিনতে পারছিনে! মনে হচ্ছে বিয়ের কনে! কী সুন্দরই মানিয়েছে, দেখ দেখ।’ বলিয়াই আয়না লইয়া মুখের কাছে ধরিল।
ভূণী মুখ সরাইয়া লইয়া বলিল, ‘যাও! তা হলে সব খুলে ফেল বলছি! আমি কিছুতেই বাইরে যেতে পারব না। মা গো! কেন এ সব পরলুম!’
সে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিল!
জাহাঙ্গীর বাহির হইতে বলিল, ‘কী হচ্ছে হারুণ? তুমিও তো কম দুষ্টু নও!’
হারুণ হাসিয়া বলিল, ‘জাহাঙ্গীর! তোমার পাওনা সালামটা নিতে তুমিই ভিতরে এসো ভাই। ও বলেছে, এ রকম করে সেজে কিছুতেই বাইরে যাবে না। অর্থাৎ কিনা তোমার সামনে বার হবে না।’
জাহাঙ্গীর হাসিয়া ভিতরে যাইতেই ভূণী একবার তাহার দিকে তাকাইয়াই তাহার মায়ের বিছানায় বসিয়া পড়িয়া বালিশে মুখ লুকাইল। জাহাঙ্গীর কেমন যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল।
হারুণ ভূণীর মুখ জোর করিয়া তুলিয়া বলিল, ‘ওরে, একবার দেখা ভালো করে! আর, যে সালামের লোভে জাহাঙ্গীর বেচারা পা দুটোকে ভিতরবাড়ি পর্যন্ত টেনে আনলে, তার থেকেই বঞ্চিত করলি বেচারাকে? ওঠ, সালাম কর।’
কিন্তু উঠাইতে গিয়া হারুণ দেখিল, চোখের জলে ভূণীর মুখ ভাসিয়া গিয়াছে। সেই অশ্রুসিক্ত চোখ না মুছিয়া সে যেমন জাহাঙ্গীরকে সালাম করিতে যাইবে, অমনি এক অভাবনীয় কাণ্ড হইয়া গেল!
ভূণীর উন্মাদিনী মাতা এতক্ষণ উদাস নির্বিকার চক্ষে সমস্ত দেখিতেছিলেন। কিছু বুঝিতেছিলেন বলিয়া বোঝা যাইতেছিল না।
ভূণীর উন্মাদিনী মাতা এতক্ষণ উদাস নির্বিকার চক্ষে সমস্ত দেখিতেছিলেন। কিছু বুঝিতেছিলেন বলিয়া বোঝা যাইতেছিল না।
মাথার ওপর বজ্রপাত হইলেও বুঝি সকলে এমন স্তম্ভিত হইত না! হারুণ, জাহাঙ্গীর, ভূণী ওরফে তহমিনা সকলে যেন প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছে।
হঠাৎ ভূণীর চোখের দিকে তাকাইয়া জাহাঙ্গীর কাঁপিয়া উঠিল। সে ধরিবার পূর্বেই ভূণী মূর্ছিতা হইয়া তাহার স্কন্ধে এলাইয়া পড়িল!
উঠানের আমগাছটায় বসিয়া একটা পাপিয়া পাখি ডাকিয়া উঠিল, চোখ গেল! চোখ গেল! উঁহু উঁহু চোখ গেল!
কুহেলিকা – ০৯
কালবৈশাখীর মেঘ এমনি করিয়াই দেখা দেয়। যেখানে দুঃখের বরষা, বজ্রপাতও হয় সেইখানেই। শান্ত নদীতীরে তারও চেয়ে শান্ত ভগ্নকুটির এমনি করিয়াই কোনো এক দুর্যোগের নিশীথে ভাসিয়া যায়!
দুঃখ যে কত বড়ো বন্ধুর রূপ ধরিয়া আসে, হারুণ তাহাই ভাবিতেছিল – একাকী দাওয়ায় বসিয়া।
অন্ধ পিতা এক মনে কলিকার পর কলিকা তামাক পোড়াইতে ছিলেন। অগ্নিগিরির গর্ভ হইতে যে ধূম্রপুঞ্জ নির্গত হয়, তাহার জ্বালাও বুঝি এত ভয়াবহ নয়। ঘর পোড়ে, সকলে দেখে, পোড়ারও অবধি আছে; কিন্তু মনে যদি একবার আগুন লাগে – তাহা কেহ দেখেও না, তাহার অন্তও নাই।
মোমি তাহার সিল্কের শাড়ি খুলিয়া ফেলিয়া আবার সেই ছিন্ন মলিন শাড়িটি পরিয়া গৃহকর্মে রত হইয়াছে। ওইটুকু মেয়ে, তাহার এই দুঃখ ঢাকিবার কঠোর প্রয়াস দেখিয়া অশ্রু সংবরণ করা দায় হইয়া উঠে! এ যে কত বড়ো দুঃখ, কোথা দিয়া কী হইল, সে হয়তো ভালো করিয়া বুঝিতেই পারে নাই। তাহার চারিপাশে সে যেন কাহাদের দীর্ঘশ্বাস, কাহাদের নিঃশব্দ ক্রন্দন অনুভব করিতেছে। কীসের এ বিষাদ, সে তাহা জানে না! তাহাকে সবচেয়ে বেশি বেদনা দিয়াছে – জাহাঙ্গীরের আজই কলিকাতা চলিয়া যাওয়ার আয়োজন!
উন্মাদিনী মাতা অঘোরে ঘুমাইতেছেন – উন্মাদিনী নিয়তির মতোই নির্বিকার নিশ্চিন্ত আরামে!
ভূণী তাহার সকালের-পরা সাজসজ্জা লইয়া পাষাণ-প্রতিমার মতো বসিয়া আছে। হারুণ একবার চুপি চুপি তাহাকে ও অলক্ষুণে বস্ত্র খুলিয়া ফেলিতে বলায় সে অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছিল, ‘ওকে যেতে দাও ভাই, তার পর চিরকালের জন্যই খুলে ফেলব!’ ইহার পর হারুণ আর কিছু বলিতে সাহস করে নাই।
দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। জাহাঙ্গীর সমস্ত বাঁধিয়া ছাঁদিয়া সহজ শান্তভাবে হারুণদের আঙিনায় আসিয়া দাঁড়াইল। হারুণ তাহাকে কিছু বলিবার আগেই ভূণী ভিতর হইতে ডাকিল, ‘মেজোভাই, শুনে যাও।’
হারুণ জাহাঙ্গীর দু-জনারই বুক কাঁপিয়া উঠিল।
ভূণী তাহার সেই বধূবেশ লইয়া অকুতোভয়ে বাহিরে আসিয়া বলিল, ‘বা-জান! তুমি দলিজে যাও তো একটু!’
ইহা যেন অনুরোধ নয়, আদেশ।
মনে হইল, অন্ধ পিতা সব বুঝিয়াছেন। মোবারককে ডাকিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।
জাহাঙ্গীরের ভয় করিতে লাগিল, বুঝি মাতার মতো কন্যারও মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটিয়াছে। সে আঙিনায় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিল – নিজের জন্য নয়; এই হতভাগিনির দুঃখে! তাহার জীবনদেবতা জীবন লইয়া কী খেলা খেলেন, তাহা দেখিবার জন্য সে নিজেকে অম্লান বদনে তাঁহার হাতেই সঁপিয়া দিয়াছে। আজিকার বজ্রপাতকেও সে তাই মাথা পাতিয়াই গ্রহণ করিবে!
ভূণী একটু জোরেই হারুণকে বলিল, ‘মেজোভাই, আমি তোমার বন্ধুর সাথে দুটো কথা বলতে পারি?’
হারুণ অবাক হইয়া ভূণীর মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।
ভূণী তেমনই সতেজ কণ্ঠেই বলিয়া উঠিল, ‘বুঝেছি মেজোভাই, তুমি কী ভাবছ। কিন্তু ভাববার কিছুই নেই এতে। আমার মঙ্গল-অমঙ্গলের কথা আমার চেয়ে কেউ বুঝবে না। আমি তোমারই তো ছোটো বোন। আমায় দিয়ে অন্যায় কিছু হবে না, এ তুমি জেনে রেখো। আমি আমার দুর্ভাগ্যের শেষটুকু জেনে নিতে চাই।’
হারুণের দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, সে আর দাঁড়াইতে পারিল না। সে চোখের জল মুছিতে মুছিতে তাহার মাতার পায়ের কাছে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল।
ভূণী জাহাঙ্গীরের চোখের দিকে চাহিয়া জড়িতকণ্ঠে বলিল, ‘আপনার সঙ্গে দুটো কথা আছে, একটু ভিতরে এসে বসবেন?’
জাহাঙ্গীর কলের পুতুলের মতো সে আদেশ পালন করিল।
ভূণী একেবারে জাহাঙ্গীরের পায়ের নীচে বসিয়া পড়িয়া অশ্রু-টলমল ডাগর চক্ষু দুটি ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, ‘আপনি কি এখনই চলে যাচ্ছেন?’
জাহাঙ্গীর তাহার পা চৌকিতে তুলিয়া তো লইলই না, কোনোপ্রকার অসোয়াস্তির ভাবও তাহার ব্যবহারে ফুটিয়া উঠিল না। সহজ শান্ত কণ্ঠেই সে বলিয়া উঠিল, ‘হাঁ ভাই, আমি যাচ্ছি!’ একটু থামিয়া বলিল, ‘দুঃখের পসরা খোদা আমার মাথায় তুলে দিয়েছেন, তার জন্য দুঃখ করিনে ভাই, কিন্তু এর তাপ যে অন্যের গায়ে গিয়ে লাগে, এ দুঃখ রাখবার আর ঠাঁই নাই। আমি এসেছিলাম দুঃখ ভুলতে, কিন্তু সে দুঃখ যে এত বিপুল হয়ে উঠবে, সে দুঃখ যে অন্যেরও ঘর পোড়াবে – এ আমি জানতাম না।’
ভূণী একটু হাসিয়া শাড়ির আঁচলটায় পাক দিতে দিতে মুখ না তুলিয়াই বলিল, ‘সত্যই কি তাই? আপনাদের বড়োলোকের কি কোনোরকম দুঃখবোধ আছে?’
জাহাঙ্গীর আহত হইয়া বলিয়া উঠিল, ‘ও কথা কেন বলছ ভাই? আমরা তোমার কথায় “বড়োলোক” হলেও মানুষ। অন্তত আমার হৃদয় নেই – এমন কিছুরই হয়তো পরিচয় দিইনি এখনও।’
ভূণী তেমনই ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, ‘দেন নাই, পরে দেবেন! আচ্ছা, আপনি তো মহৎ হৃদয়বান এবং সেইজন্যই হয়তো তাড়াতাড়ি পালিয়ে যাচ্ছেন। আপনি স্বেচ্ছায় এসেছেন, স্বেচ্ছায় যাবেন, এতে কারই বা বলবার কী আছে। কিন্তু আমার কী হবে, বলতে পারেন?’ – আবার সে তাহার দুই আয়ত লোচনের অশ্রুর আবেদন জাহাঙ্গীরের পানে তুলিয়া ধরিল!
জাহাঙ্গীর একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, ‘আমি বুঝেছি ভূণী, আজ কী সর্বনাশ হয়েছে! কিন্তু তুমিও কি এত বড়ো মিথ্যাটাকেই সত্য বলে গ্রহণ করলে? পালিয়ে আমি যাচ্ছি না, আমি যাচ্ছি এই লজ্জার হাত এড়াতে। হারুণ আমার কত বড়ো বন্ধু, তা হয়তো তুমি জান না। আমার হাত দিয়েই তোমাদের এত বড়ো লাঞ্ছনা ছিল, তা আমি জানতাম না। কিন্তু তুমি তো জান, এতে আমাদের কারুরই অপরাধ নেই। অপরাধ শুধু আমার দুরদৃষ্টের!’
ভূণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ‘দূরদৃষ্ট শুধু আপনার নয়, আমার। যে আগুন লাগায়, সে জানে না যার বুকে আগুন লাগল – তার কতটুকু পুড়ল! সে যাক, আপনি যেটাকে মিথ্যা বলছিলেন, আপনি বোধ হয় জানেন না, সেটার চেয়ে বড়ো সত্য আমার কাছে নেই! আপনি বলবেন, মা আমার উন্মাদিনী। তবু তিনি আমার মা। আমরা নারী, আমরা হয়তো সকল কিছু অন্ধের মতো বিশ্বাস করি। খোদার ইঙ্গিত না থাকলে এ অভাবনীয় দুর্ঘটনা আমার উন্মাদিনী মায়ের হাত দিয়ে ঘটত না!’ তাহার পর একটু থামিয়া সে শান্তকণ্ঠে বলিল, ‘আমি খুলেই বলি আপনাকে, মা যার হাতে আমায় সঁপে দিয়েছেন, তার চেয়ে বড়ো সত্য আমার কাছে নেই!’
জাহাঙ্গীরের মনে হইতে লাগিল, পৃথিবীর চন্দ্রসূর্য সমস্ত ডুবিয়া গিয়াছে। একাকী অন্ধকারে সে অতল হইতে অতলতর গহ্বরে তলাইয়া যাইতেছে।
কিন্তু সে মুহূর্তকালের জন্য। একটু পরেই সে সামলাইয়া উঠিল। সে আর কিছু বলিতে যাইবার পূর্বেই ভূণী ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, ‘আপনি যা বলবেন তা আমি জানি। ফাঁসির আসামি যেমন করে তার দণ্ডাজ্ঞা শোনে, আপনার কাছ থেকে হয়তো তেমনি করেই তেমনই কঠোর কিছুই শুনতে হবে; আমি তার জন্য প্রস্তুত আছি। তবুও আমি আমার যা বলবার বললাম। আপনি আমায় পাগল বা ওই রকম অদ্ভুত কোনো কিছু ভাবছেন, না?’ – আবার সেই অস্তমান শশীকলার মতো কান্নাভরা হাসি!
জাহাঙ্গীর এতক্ষণে তাহার পরিপূর্ণ দৃষ্টি দিয়া ভূণীর দিকে তাকাইয়া দেখিল। তাহার চকচকে চোখ নিমেষে ব্যথায় ম্লান হইয়া উঠিল। ওই নিমেষের দৃষ্টি বিনিময়। তাহার মনে হইল, ওই অপূর্ব সুন্দর দুইটি চক্ষুর জন্যই সে সর্বত্যাগী হইতে পারে!… হঠাৎ তাহার সুপ্ত আহত অভিমান যেন নিদ্রোত্থিত কেশরীর ন্যায় জাগিয়া উঠিল। বন-হরিণীর মতো চক্ষু ইহাদের, হরিণীর মতোই মায়াবী ইহারা, তবু ইহারা শিকারের জীব! ইহাদের হত্যা করায় পৌরুষও নাই, করিলে লজ্জাও নাই! তাহার মনে হইতে লাগিল, সে জাহাঙ্গীর নয় – সে শুধু মদ্যপ চরিত্রহীন ফররোখ সাহেবের পুত্র!
এইবার সে একটু বক্র-হাসি হাসিয়াই বলিল, ‘তোমার মা উন্মাদিনী হলেও তোমায় তা ভাবতে পারি না ভূণী। আর কোনো মেয়ে হলে তাকে ধূর্ত বলতাম – প্রগল্ভা না বলে; কিন্তু তোমায় তা বলতে আমার মতো কশাই-এরও বাধবে! আমার কপালই এই রকম। যারাই আমার জীবনে বিপর্যয় এনেছে, তাদের সকলেই অদ্ভুত এক-একটি জীব। কিন্তু সে কথা যাক। তুমি এখনই বলছিলে – ফাঁসির আসামির মতোই আমার দণ্ডাজ্ঞা শুনতে প্রস্তুত আছ। আমি যদি সত্যিসত্যিই তোমার যাবজ্জীবন নির্বাসনের দণ্ডাজ্ঞা দিই, তুমি তা সইতে পারবে?’ বলিয়াই নিষ্ঠুরের মতো হোহো করিয়া হাসিয়া উঠিল।
ভূণী মুহূর্তের জন্য অন্তরে কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার পরেই সে গলবস্ত্র হইয়া জাহাঙ্গীরের পায়ে হাত দিয়া সালাম করিয়া বলিল, ‘আপনার ওই দণ্ডাজ্ঞা গ্রহণ করলাম!’ তাহার পর ভিতরে চলিয়া যাইতে যাইতে বলিল, ‘অনেক অদ্ভুত জীবই তো দেখেছেন জীবনে, এবং সে জীব-হত্যায় আপনার হাতযশও আছে মনে হচ্ছে, এইবার আরেকটা জীব দেখে গেলেন! কিন্তু মনে রাখবেন, যাদের জীব-হত্যাই পেশা, তাদের সে ঋণ একদিন শোধ করতে হয় ওই বন্যজীবের হাতেই!’ – সে রানির মতো সগর্বে চলিয়া গেল।
জাহাঙ্গীর একটু চিৎকার করিয়াই বলিয়া উঠিল, ‘আমার শেষ কথা শুনে যাও তহমিনা, নইলে আমায় নিয়ে সবচেয়ে বড়ো দুঃখ পোহাতে হবে তোমার!’ ভূণী ভিতর হইতে বলিল, ‘আমি এখান থেকেই আপনার চিৎকার শুনতে পাচ্ছি বলুন।’
জাহাঙ্গীর সহসা এই ব্যঙ্গোক্তিতে ক্রুদ্ধ হইলেও তাহার অপূর্ব আত্মসংযমের বলে কণ্ঠ যথাসম্ভব শান্ত করিয়া বলিল, ‘আমি প্রেমও বিশ্বাস করিনে, পৃথিবীর কোনো নারীকেও বিশ্বাস করিনে! মনে হচ্ছে, তোমার সব কথাই আর-কারুর শেখানো, অথবা ও-গুলো অতিরিক্ত নভেল পড়ার বদহজম! তোমাদের জাতটারই নির্বাসন হওয়া উচিত। একেবারে কালাপানি!’
ভূণী রেকাবিতে করিয়া এক রেকাবি সন্দেশ ও এক গ্লাস পানি লইয়া জাহাঙ্গীরের সামনে রাখিতে রাখিতে সহজ কণ্ঠেই বলিল, ‘আপনি বড্ড দুর্মুখ! যাবেনই তো, যাবার সময় একটু মিষ্টিমুখ করে যান।’ বলিয়াই সে হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, ‘মাফ করবেন, আপনার দেওয়া মিষ্টি দিয়েই আপনার তেতো মুখ মিষ্টি করতে হচ্ছে! জানেনই তো, আমরা কত গরিব! তাতে আবার পাড়াগেঁয়ে। একটা ঘরের মিষ্টি দিয়ে আপনার জমিদারি মুখের ঝাল মিটাতে পারলাম না! আপনি খান, আমি দুটো পান সেজে আনি।’ বলিয়াই সে ভিতরে চলিয়া গেল।
জাহাঙ্গীর আর একটি কথাও না বলিয়া সুবোধ বালকের মতো রেকাবির মিষ্টি গলাধঃকরণ করিতে লাগিল। তাহার আজ কেবলই মনে হইতে লাগিল, মিষ্টি যে এত মিষ্টি হয় – তাহা সে জীবনে উপলব্ধি করে নাই, হয়তো আর কখনও করিবেও না। কিন্তু এই নারী, এই প্রগল্ভা তরুণী! এ কোথা হইতে আসিল? বনফুলের এই সৌন্দর্য, এত সুবাস! গহন বনের অন্ধকারে এ কোন কস্তুরীমৃগ তাহার মেশ্ক-খোসবুতে সারা বন আমোদিত করিয়া তুলিতেছে? কয়লার খনিতে এ কোন কোহিনূর লুকাইয়া ছিল? জাহাঙ্গীর যেন দিশা হারাইল। সে জাহাঙ্গীর নয়, বিলাসী ফররোখ সাহেবের পুত্র নয়, সে ‘শিভালরি’ যুগের বীরনায়ক, বিংশ শতাব্দীর সভ্য যুবক! সে এই মহীয়সী নারীর অবমাননা করিবে না! আপনার অজ্ঞাতেই তাহার কণ্ঠ দিয়া উচ্চারিত হইল, ‘তহমিনা! তহমিনা!’
ভূণী তশতরীতে পান লইয়া আসিতেছিল। জাহাঙ্গীরের এই অস্বাভাবিক স্বরে একটু বিস্ময়ান্বিত হইয়াই সে নিকটে আসিয়া বলিল, ‘আমায় ডাকছিলেন?’
জাহাঙ্গীর অপ্রতিভ হইয়া ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল, ‘না?’ জাহাঙ্গীর নিজেই চমকিত হইয়া উঠিল। তাহার নিজের কণ্ঠস্বরে যে এত মধু আছে তাহা সে নিজেও জানিত না।
ভূণী স্নেহ-গদগদ কন্ঠে বলিয়া উঠিল, ‘এই তো বেশ লক্ষ্মী ছেলের মতো সব মিষ্টিই খেয়েছেন দেখছি। দেখুন, আপনি বড্ড বদরাগী! হয়তো আপনার কোনো অসুখ-বিসুখ আছে, দোহাই! কলকাতা গিয়ে একটু চিকিৎসা করাবেন!’ বলিয়াই হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, ‘তাই তো বলি, যে লোক দু-হাতে এত হাঁড়ি হাঁড়ি মিষ্টি বিলাতে পারে, তার মেজাজ কি এত তেতো হয়? আর দুটো মিষ্টি এনে দেই, লক্ষ্মীটি, “না” বলবেন না। সেই কখন দুপুর রাত্তিরে কলকাতা পৌঁছোবেন, আর খিদের চোটে রাস্তায় হয়তো কাউকে খুন করেই বসবেন! যা মেজাজ, বাপরে!’ বলিয়াই জাহাঙ্গীরের দিকে গভীর সানুরাগ দৃষ্টি দিয়া তাকাইতেই দেখিল, জাহাঙ্গীর মুখে ক্রমাগত পান ঠাসিতেছে।
ভূণী এবার ছেলেমানুষের মতো তরল কণ্ঠে চেঁচাইয়া উঠিল, ‘অ মা! কী হবে! পান খেয়ে ফেলেছেন? ফেলে দিন, ফেলে দিন! বেশ! ফেলবেন না তো!’ বলিয়াই বহুদিনের রোগক্লান্ত রুগির মতো শান্তকণ্ঠে বলিতে লাগিল, ‘চির-নির্বাসনই তো দিয়ে গেলেন। আপনাকে যতটুকু জেনেছি, তাতে এ আমার ধ্রুব ধারণা যে, আর আমাদের কোনোকালেই দেখা হবে না।’ তাহার পরে একটু থামিয়া চোখমুখ ডাঁশা আপেলের মতো লাল করিয়া সলজ্জকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ‘আমাদের যদি আজ সত্যিসত্যিই বিয়ে হয়ে যেত, তাহলে এক বছরেও হয়তো এত কথা এমন করে বলতে পারতাম না আপনার কাছে। দুর্দিন মানুষকে এমনই বেহায়া করে তোলে! আমার যে এক মুহূর্তেই জীবনের সাধ মিটিয়ে ফেলতে হবে। আমার মতো দুর্ভাগিনি এক কারবালার সকিনা ছাড়া বুঝি কেউ নেই!’ বলিয়াই সে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ভিতরে চলিয়া গেল!
জাহাঙ্গীরের কেবলই মনে হইতে লাগিল সে বুঝি ইহজগতে নাই। সে যেন স্বপ্ন দেখিতেছে। তাহার সমস্ত অঙ্গ যেন কাহার অভিশাপে প্রস্তরীভূত হইয়া যাইতেছে! সে না পারিল নড়িতে, না পারিল একটা বাক্য উচ্চারণ করিতে! কিন্তু তাহার আর বিস্ময়ের অবধি রহিল না, যখন সে দেখিল, অল্প পরেই ভূণী আর এক রেকাবি সন্দেশ লইয়া তাহার সম্মুখে রাখিতেছে। তাহার মনে হইল, কে যেন জাদু করিয়া তাহাকে এই রহস্যপুরীতে বন্দি করিতেছে! সে যেন সকল দেশের সকল গল্প-কাহিনির নায়ক – রূপকুমার। হঠাৎ সে অভিভূতের মতো বলিয়া ফেলিল, ‘তহমিনা! তুমি আমার সাথে যাবে? জানি না, তুমি কারবালার সকিনা, না, সিস্তানের তহমিনা। বলো, তুমি যাবে?’
ভূণী দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, ‘না!’
জাহাঙ্গীরের স্বপ্ন টুটিয়া গেল। সে আবার বহুক্ষণ ধরিয়া ভূণীকে দেখিল। দেখিয়া যখন সাধ মিটিতে চায় না; হায় রে ভুখারি অবিশ্বাসী চোখ! তবু সে জিজ্ঞাসা করিল, ‘কেন যাবে না? তুমিই না বলছিলে, তোমার মা যার হাতে তোমায় সঁপে দিয়েছেন, তার চেয়ে বড়ো সত্য তোমার আর নেই।’
ভূণী মৃদুকণ্ঠে বলিল, ‘এখনও তাই বলছি। তবু এমন করে তো যাওয়া যায় না। আপনাকে আমি উপদেশ দিতে পারি, এত বড়ো স্পর্ধা আমার নেই। আমার অন্তরের সত্য যত গভীরই হউক, তবু তাকে সমাজের কাছে রং বদলিয়ে নিতে হবে। নইলে কেউই সুখী হতে পারব না।’
জাহাঙ্গীর অনেকক্ষণ ধরিয়া কী ভাবিল, তাহার পর কম্পিত কণ্ঠে বলিল, ‘তা হতে পারে না ভূণী, আমি এতক্ষণ ভুল বকছিলাম। আমায় ক্ষমা করো। যে প্রেমে অবিশ্বাস করে, তার মতো হতভাগ্য বুঝি বিশ্বে কেউ নেই। তার কোথাও কোনো কিছুতেই সুখ নেই। আমায় নিয়ে তুমি সুখী হতে পারবে না, আমিও তোমায় নিয়ে – শুধু তোমায় বলে নয় – কোনো নারীকে নিয়েই সুখী হতে পারব না। যে সত্যকে আমি চোখের সামনে দেখি, তাকেও বিশ্বাস করতে পারিনে, আমার রক্তে রক্তে যেন প্রতিধ্বনি ওঠে, ভুল, ভুল, এ সব মিথ্যা, ছলনা! আমি তোমায় আমারও অজানিতে দুঃখ দিয়ে গেলাম। কিন্তু তুমি তো জান – আমার অপরাধ কতটুকু! তোমার কোনোদিন কোনো উপকার করেও যদি আমার এ অনিচ্ছাকৃত অপরাধের লাঘব করতে পারি, তবে নিজেকে ধন্য মনে করব – শুধু এইটুকুই মনে রেখো। আমার আর সব ভুলে যেয়ো!’ শেষের কথা কয়টি বলিবার সময় তাহার কণ্ঠ যেন ভাঙিয়া আসিতেছিল! – সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া বলিল, ‘তবে যাই এখন!’
ভূণী ভগ্নকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ‘অনুগ্রহ করে আপনার এই কাপড় কয়খানা নিয়ে যান! একটু বসুন, আমি আসছি।’
জাহাঙ্গীর চলিয়া যাইতেছিল! ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, ‘আমি তো তোমায় নির্বাসনই দিলাম, ওই শাড়ি তোমার জেলের পোশাক!’
তহমিনা সেইখানেই ছিন্নকণ্ঠ কপোতীর মতো লুটাইয়া পড়িয়া ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, ‘আমি পারব না, পারব না এ শাস্তি বইতে! নিষ্ঠুর, আমায় তুমি প্রাণদণ্ড দিয়ে যাও, এ নির্বাসন দিয়ো না , দিয়ো না!’
দুটো পাপিয়ায় তখনও আঙিনায় যেন আড়াআড়ি করিয়া ডাকিতেছিল, ‘পিউ কাঁহা! পিউ কাঁহা! চোখ গেল, চোখ গেল!’
কুহেলিকা – ১০
সন্ধ্যার পূর্বেই জাহাঙ্গীর গোরুর গাড়িতে চড়িয়া শিউড়ি চলিয়া গেল।
সন্ধ্যার বিষণ্ণতা এমন করিয়া বুঝি আর কখনও নামে নাই হারুণদের বাড়িতে।
ভূণীর যখন জ্ঞান হইল, তখন তাহার সর্বপ্রথম এই প্রার্থনাই অন্তর ভরিয়া গুমরিয়া ফিরিতে লাগিল, ‘ধরণি দ্বিধা হও! এ মুখ যেন আর দেখাইতে না হয়!’
সেও কি সত্যসত্যই তাহার মাতার ন্যায় উন্মাদিনী হইল? নহিলে এত কথা এমন লজ্জাহীনার মতো সে বলিল কেমন করিয়া?… সন্ধ্যার এ অন্ধকার যেন আর না কাটে! সে আর আলোকের মুখ দেখিতে পারিবে না।
কেহ সন্ধ্যা-দীপ জ্বালিলও না। কেহ জ্বালিতেও বলিল না। আলো জ্বলিয়া উঠিলে বুঝি এ বেদনা এ লজ্জার কালিমা দ্বিগুণতর হইয়া দেখা দিবে।
বাড়ির প্রত্যেকেই যেন প্রত্যেকের কাছে অপরাধী!
উন্মাদেনী মাতার আবোল-তাবোল বকুনির মাঝে ক্রন্দনও শোনা যাইতেছিল, ‘মিনা আমার! বাপ আমার! এসে আবার চলে গেলি?’
হারুণ এতক্ষণ একটি পুকুরের নির্জন পাড়ে বসিয়া আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতেছিল। জাহাঙ্গীরের তো কোনো অপরাধই নাই। কিন্তু নাই বা বলি কেমন করিয়া? সে কেন এ দরিদ্রের বাড়ি আসিতে চাহিল? যদি আসিলই এবং দৈবক্রমে এ দুর্ঘটনা ঘটিলই যদি, সে কেন ইহার মীমাংসা করিয়া গেল না? হতে পারে, তাহারা দরিদ্র, কিন্তু বংশ গৌরবে তাহারা তো একটুও খাটো নয়। আর ওই ভূণী, অমন অপরূপ সুন্দরী, অপূর্ব বুদ্ধিমতী মেয়েও কি তাহার বধূ হইবার অযোগ্য? তাহাকে যে অবহেলা করিয়া গেল, এই বেহেশ্তী ফুলের মালাকে যে পদদলিত করিয়া গেল, সে কি মানুষ? ভালোই হইয়াছে, ওই হৃদয়হীন বাঁদরের গলায় এ মুক্তার মালা শোভা পাইত না বলিয়াই এ অঘটন ঘটিয়া গেল!… কিন্তু ভূণী! উহার কী হইবে? জাহাঙ্গীরের সাথে তাহার সমস্ত কথাই সে শুনিয়াছে, ভূণীকে সে ভালো করিয়াই চিনে। সে ভাঙিবে কিন্তু নোয়াইবে না! সে ভয় করিতে লাগিল, এইবার তাহার অন্ধ পিতা আর বাঁচিবে না!
হঠাৎ তাহার মনে হইল জাহাঙ্গীরের বিদায়-ক্ষণের কথা। সে হারুণকে আড়ালে ডাকিয়া বলিয়াছিল, ‘আমার সব কথা শুনলে তুমিই আমায় তোমার বোন দিতে রাজি হবে না হারুণ!’ হারুণ পীড়াপীড়ি করাতে সে বলিয়াছিল, ‘সব কথা আমার বলতে চাইনে ভাই। হয়তো বা আামার সব কথা আমি নিজেই জানিনে। কিন্তু আমার যেটুকু কৃতকর্মের জন্য আমি দায়ী, অন্তত সেইটুকু শুনলেই তোমার রক্ত হিম হয়ে যাবে!… আমি খুলেই বলি, আমি বিপ্লবী।’
চলিতে চলিতে হঠাৎ গোখরো সাপের গায়ে পা পড়িলে – মানুষ যেমন চমকাইয়া ওঠে, হারুণ তেমনই চমকিয়া উঠিয়া বলিয়াছিল, ‘জাহাঙ্গীর, তুমি – তুমি – বিপ্লবী?’
অবশ্য, বিপ্লবী – রিভোলিউশনারি যে কোন ভয়ানক জীবকে বোঝায় তাহা সে স্পষ্ট করিয়া জানিত না। আর স্পষ্ট করিয়া জানিত না বলিয়াই, তাহার অত ভয়! ভূত দেখা যায় না বলিয়াই না লোকের এত ভূতের ভয়! হারুণ ছেলেবেলা হইতেই একটু অতিরিক্ত ভীরু। আজও সে রাতে একা ওঠা তো দূরের কথা – একা ঘরে শুইতেও ভয় করে। কাজেই চোখের সামনে একজন বিপ্লবীকে দেখিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, সে সত্য সত্যই ভূত দেখিতেছে! সে জানিত বিপ্লবীদের তাহারা তো দূরের কথা, সি.আই.ডি পুলিশেও দেখিতে পায় না! উহারা আকাশলোকে অভিশাপের মতোই ধরাছোঁয়ার বহু ঊর্ধ্বে থাকিয়া বিচরণ করিয়া বেড়ায় এবং হঠাৎ বজ্রপাতের মতোই কখন শিরে আসিয়া পতিত হয়।
সে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, ‘কিন্তু বিপ্লবীরা যে ভীষণ লোক জাহাঙ্গীর! তুমি তো তা নও!’
জাহাঙ্গীর হাসিয়া ফেলিয়া বলিয়াছিল, ‘ভয় নেই হারুণ, বিপ্লবীরা তোমার আমার মতো ঘরের মানুষ, বনের বাঘ নয়! আর যদি আমাদের সত্যিই তা মনে কর, তা হলে তো তোমারই এ বিয়েতে সর্বপ্রথম অসম্মত হওয়া উচিত! কিন্তু আসল কথা কী জানো হারুণ, আমি বিয়ে করতে পারি না, আমাদের বিয়ে করতে নেই!’
হারুণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো জাহাঙ্গীরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।
জাহাঙ্গীর হঠাৎ একটু কর্কশ কণ্ঠেই বলিয়া উঠিল, ‘তুমি এত বেশি ভীরু, তা আমি জানতাম না হারুণ। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে তোমায় আমার এ পরিচয় দিয়ে ভালো করিনি। আমরা সত্যিসত্যিই বাঘের চেয়েও ভীষণ – কিন্তু শুধু তারই জন্য যে বিশ্বাসঘাতকতা করে। আমি যে কথা তোমায় বললাম তা ঘুণাক্ষরেও যদি প্রকাশ পায়, তা হলে বন্ধু’ – বলিয়াই সে বুকের তলা হইতে যে অস্ত্র বাহির করিয়া দেখাইল, তাহাতে হারুণ পতনোন্মুখ বংশপত্রের মতো কাঁপিতে লাগিল!
জাহাঙ্গীর পরক্ষণেই হাসিয়া তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, ‘আশা করি – কোনো দিনই এর প্রয়োজন হবে না বন্ধু। অনেক দুঃখ দিয়ে গেলাম, তবে এর এক কণা ঋণও যদি পরিশোধ করতে পারি কোনোদিন, তা হলে আমার মনের অনুশোচনা অনেক কমে যাবে।… আর দেখ, তুমি একটু চেষ্টা করলেই ভূণী সব ভুলে যাবে। হাজার হোক সে ছেলেমানুষ বই তো নয়! তা ছাড়া মা উন্মাদিনী হলে ছেলেমেয়ে একটু অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ হয়। তবে, এ মাটির পৃথিবীতে ও সব টেকে না ভাই, এই যা ভরসার কথা!’
শেষের দিককার কথা কয়টার নিষ্ঠুরতা ও বিরসতা হারুণকে গভীরভাবে বাজিলেও সে শুষ্ককণ্ঠে কোনোরকমে বলিয়াছিল, ‘তা হলে এসো ভাই! আশা করি, এর পরেও আমরা বন্ধু থাকব!’ জাহাঙ্গীর ‘নিশ্চয়’ বলিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিল।
হারুণ কেবলই ভাবিতে লাগিল, একটা লোকই একসঙ্গে এত ভালো এবং এত মন্দ কী করে হতে পারে!
এমন সময় অন্ধ পিতার ডাক শুনিয়া হারুণের দুঃস্বপ্ন টুটিয়া গেল। ভিতরে ঢুকিয়া সে একটু উচ্চকন্ঠেই বলিয়া উঠিল, ‘আজ কি বাতি জ্বলবে না বাড়িতে?’
ভূণী উঠিয়া আলো জ্বালিতে চলিয়া গেল।
হারুণ দাওয়ায় উপবিষ্ট তাহার পিতার নিকট বসিয়া পড়িল, ‘আমায় ডাকছেন আব্বা!’
অন্ধ পিতা ক্লান্তকণ্ঠে বলিলেন, ‘হুঁ!’ তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন, ‘এখন কী করা যায় – ঠিক করলে কিছু?’
হারুণ নম্রস্বরে বলিল, ‘এর কী আর ঠিক করবার আছে?’
তাহার পিতা উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, কিছু করবার নাই? বেশ! তোমার কিছু না থাকতে পারে কিন্তু আমার আছে। আমি পিতা হয়ে চোখের সামনে মেয়ের সর্বনাশ দেখতে পারব না। আমি কালই জাহাঙ্গীরের মাকে সব কথা জানিয়ে চিঠি দেব। দেখি, উনি কী বলেন, তারপর আমরা যা করবার করব।’
হারুণ মিনতি-ভরা কণ্ঠে বলিল, ‘না আব্বা, তা তুমি করতে পারবে না। ওতে আমাদের মান-ইজ্জতের হানি ছাড়া লাভ কিছু হবে না।’
অন্ধ পিতা বহুক্ষণ ধরিয়া কী চিন্তা করিতে লাগিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন, ‘তুমি ঠিকই বলেছ বাবা, কিন্তু এ ছাড়া তো উপায়ও দেখছি না। তুই তো জানিস হারুণ, ভূণী কেমন ধাতের মেয়ে। ওকে কি কেউ বিয়ে দিতে পারবে মনে করিস? তোর কাছে যা শুনেছি, তাতে মনে হয়, জাহাঙ্গীরের মার সত্যিকারের বুদ্ধিসুদ্ধি আছে, হৃদয়ও আছে। আমার এই দুঃখের কাহিনি শুনলে তিনি ছেলেকে বুঝিয়ে এর একটা সমাধান করবেনই।’
হারুণ বলিল, ‘তুমি জাহাঙ্গীরকে চেন না আব্বা, ওর মা কেন ওর বিধাতা এসেও ওকে টলাতে পারবে না। তুমি ও-চেষ্টা কোরো না।’
পিতা অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়া উঠিলেন, ‘তুই থাম হারুণ, তুই আমার চেয়ে বেশি বুঝিস না। ভূণীর কপাল যদি পুড়েই থাকে, তা হলে ভালো করেই পুড়ুক! আমিও আমার দুঃখের শেষ সীমা দেখে নিই! তারপর উপরে খোদা আছেন, আর পায়ের নীচে তো গোর আছেই।’
কুহেলিকা – ১১
জাহাঙ্গীরের জীবনে এই প্রথম গোরুর গাড়ির অভিজ্ঞতা।
জাহাঙ্গীর যখন বলিল, সে কিছুতেই তাহার বোঝা আর এক জন মানুষের অর্থাৎ কুলির মাথায় চড়াইয়া দিয়া তাহার অবমাননা করিবে না, বরং সে তাহার এই আভিজাত্যের অভিশাপ নিজেরই মাথায় তুলিয়া বাহির হইয়া যাইবে, তখন হারুণ একরকম জোর করিয়াই তাহার জন্য গোরুর গাড়ির ব্যবস্থা করিয়া দিল।
গোরুর গাড়িতে চড়িতে জাহাঙ্গীরের শহুরে সংস্কারে একটু বাধিলেও সে আর আপত্তি করিল না। একটু কৌতূহল ও যে হইল না, এমন নয়!
হারুণ হাসিয়া বলিয়াছিল, ‘আশা করি গো-জাতির প্রতি তোমার মানবত্ববোদ আজও প্রবল হয়ে ওঠেনি!’
জাহাঙ্গীরও হাসিয়া বলিয়াছিল, ‘না বন্ধু! বাঙালির বুদ্ধি আজও সেরকম আচ্ছন্ন হয়ে পড়েনি। ওরা হনুমান ও গোরুর পূজা করেনি কখনও! ওই দুটো জীব বাংলার বাইরেরই দেবতা হয়ে আছেন!…’
গোরুর গাড়িতে চড়িয়া ক্রোশ-খানেক যাইবার পর জাহাঙ্গীরের কৌতূহল ও উৎসাহ একেবারে জল হইয়া গেল। অসমান গ্রাম্যপথে ঘন্টায় প্রায় এক মাইল গতিতে সনাতন গো-যান যে বিচিত্র শব্দ করিয়া ধূলি-পটল উড়াইয়া চলিতেছিল, তাহাতে জাহাঙ্গীরের ধৈর্য ধরিয়া বসিয়া থাকা একপ্রকার অসহ্য হইয়া উঠিল। অনবরত ঝাঁকুনি খাইতে খাইতে তাহার মনে পড়িল বহু পূর্বে তাহার একবার ডেঙ্গু জ্বর হইয়াছিল, তাহাতে যে গা-হাত-পায়ের ব্যথা হইয়াছিল, সে বোধ হয় ইহার কাছে কিছুই নয়। সে আর থাকিতে না পারিয়া নামিয়া পড়াতে বেচারা গাড়োয়ান বিনয়-নম্রস্বরে বলিয়া উঠিল, ‘জি, নামলেন কেনে?’
জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, ‘তোমার “জি” সাধ করে নামলেন না বাপু, তোমার গাড়ি তাকে নামিয়ে তবে ছাড়লে।’
গাড়োয়ান গাড়ি থামাইয়া বলিল, ‘জি, গাড়িতে উঠে বসুন, আমি একুটুকু চাঁওড় করে হাঁকিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। এই শালার গোরু হুজুর একটু বেয়াড়া, তাইতে ভয় করে – কোথায় গোবোদে ফেলিয়ে দিবে। নইলে দাঁদাড়ে নিয়ে যেতুম!’
জাহাঙ্গীর হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, ‘তুমি “দাঁদাড়ে” নিয়ে চলো বাপু, আমি খানিকটা হেঁটে যাই!’ বলিয়াই গাড়ির পিছনে পিছনে আস্তে আস্তে হাঁটিয়া চলিল।
ধূলিধূসরিত জনবিরল গ্রাম্যপথ। দুই পাশে মাঠ ধু ধু করিতেছে। যেন উদাসিনী বিরহিণী। দূরে ছায়ানিবিড়পল্লি – ঝিল্লির ঘুমপাড়ানিয়া গানে যেন মায়ের কোলে শিশুর মতো ঘুমাইতেছে। জাহাঙ্গীরের মন কেমন যেন উদাস হইয়া গেল।
পথ চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল, সে যেন উদাস বাউল , না-জানার সন্ধানে এই পথে পথে গান গাহিয়া ফিরিতে আসিয়াছে। যাহারা তাহার পথে আসিতেছে পরিচিতের রূপে তাহারা তাহার কেহ নয়। যে উদাসিনীর অভিসারে সে চলিয়াছে, সে এই পল্লিবাটের না-জানা উদাসিনী। তাহাকে অনুভব করা যায়, রূপের সীমায় সে অসীমা ধরা দেয় না…
এমন সময় গাড়ির গো-বেচারি গো-যুগলকে গাড়োয়ান এমন ভাষায় সম্ভাষণ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল যাহাতে জাহাঙ্গীরের স্বপ্ন এক নিমিষে টুটিয়া গেল। হাসিতে হাসিতে সে পথের ধারেই ধুলার উপর বসিয়া পড়িল। একটু পরে পথ চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল, কেন এ দেশে এত বাউল এত চারণ এত কবির সৃষ্টি হইল। এই উদাস, তপস্বীর ধ্যানলোকের মতো শান্ত নির্জন ঘাটমাঠ যেন মানুষকে কেবলই তাহার আপন অতলতার মাঝে ডুব দিতে ইঙ্গিত করে। এ তেপান্তরে পথের মায়া যেন কেবলই ঘর ভুলায়, একটানা পুরবি সুরের মতো করুণ বিচ্ছেদ-ব্যথায় মনকে ভরিয়া তোলে, গৃহীর উত্তরীয় বাউলের গৈরিকে রাঙিয়া উঠে!…
এতক্ষণ যতবার তাহার ভূণীকে মনে পড়িয়াছে, ততবারই তাহার মন অবিশ্বাসের কালিতে কালো হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই জনবিরল উদাস প্রান্তরে আসন্ন সন্ধ্যায় চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল, এমনই একটি শান্ত পল্লিপ্রান্তে ছায়া-সুশীতল কুটির রচনা করিয়া তাহাকে লইয়া সে স্বর্গ রচনা করিতে পারে। কিন্তু তাহা হইতে পারে না! তাহার পিতার পাপ তাহার রক্তকে কলুষিত করিয়াছে। যে-কোনো মুহূর্তে সে তাহার পিতার মতোই ব্যভিচারী হইয়া উঠিতে পারে! সে জানে, তাহার রক্তের চঞ্চলতাকে, তাহার ভীষণ উদ্দাম প্রবৃত্তিকে সংযত করিতে তাহার কত বেগ পাইতে হইয়াছে। তাহার স্বর, তাহার অবয়ব, তাহার রক্ত সমস্তই ফররোখ সাহেবের। উহার মধ্যে যেটুকু জাহাঙ্গীর, তাহা এই পশুর কাছে টিকিতে পারে না। পাপই যদি করিতে হয়, পশুর কবলেই যদি আত্মাহুতি দিতে হয়, তবে সে একাই দিবে, এ পাপের সাথি অন্যকে করিবে না!
তাহার পিতার কথা ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ তাহার মাথায় যেন খুন চাপিয়া গেল। বুকের কাছে লুকানো রিভলভারটা একটানে বাহির করিয়া নিজের ললাটের কাছে ধরিল। আবার কী মনে করিয়া সেটাকে যথাস্থানে রাখিয়া দিয়া গোরুর গাড়িকে পিছনে ফেলিয়া দৃপ্তপদে পথ চলিতে লাগিল।
যাইবার সময় গাড়োয়ানের দিকে রোষ-কষায়িত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া গেল, ‘শালা, তুমি যদি তাড়াতাড়ি গাড়ি না চালাও, তাহলে এই বনের মধ্যে তোমায় মেরে পুঁতে ফেলব!’
গাড়োয়ান বেচারা ভয়ে অভিভূত হইয়া প্রাণপণে জাহাঙ্গীরের সাথে গাড়ি চালাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল! জাহাঙ্গীরের রক্তবর্ণ চোখ-মুখ দেখিয়া মনে হইল, সে ইচ্ছা করিলে সত্যসত্যই তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারে!…
শিউড়ি যখন তাহারা আসিয়া পৌঁছিল, তখন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে। গাড়োয়ান কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলিল, ‘হুজুর, বলদ দুটো আর বাঁচবে না, মর মর হয়ে গিয়েছে হুজুর! সারা রাস্তা আমি মেরে দৌড়িয়ে নিয়ে এসেছি হুজুর!’
জাহাঙ্গীর একটিও কথা না বলিয়া একটা পাঁচ টাকার নোট গাড়োয়ানের হাতে দিয়া গাড়ি হইতে সমস্ত জিনিস নিজে বহিয়া প্ল্যাটফর্মে আনিল। গাড়োয়ান এই আশ্চর্য লোকটির কোনো কিছুই যেন বুঝিতে পারিতেছিল না। সে আর গোলমাল না করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ জাহাঙ্গীর তাহাকে ডাকিয়া বলিল, ‘এই, শোন!’ বলিয়াই সে ল্যাম্পপোস্টের কাছে দাঁড়াইয়া চিঠি লিখিতে লাগিল।
চিঠি লেখা শেষ করিয়া গাড়োয়ানকে বলিল, ‘দেখ, এই চিঠি যদি ভূণীকে লুকিয়ে দিতে পারিস – তোকে দশ টাকা বকশিশ দেব। পারবি?’
গাড়োয়ান হতভম্ব লইয়া জাহাঙ্গীরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।
জাহাঙ্গীর তাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, ‘শালা হাঁদারাম! হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কী? ভূণীকে চিনিস? হারুণের বোন?’
গাড়োয়ান কম্পিতকণ্ঠে বলিল, ‘হুজুর উয়াকে চিনব না? এই তো সেদিন আমাদের কাছে ড্যাংডিঙিয়ে বড়ো হয়ে উঠল!’
জাহাঙ্গীর তাহার কাছে গিয়া কণ্ঠস্বর কমাইয়া বলিল, ‘তাকেই পৌঁছে দিতে হবে এই চিঠিটা, বুঝলি? তোর মেয়ে-টেয়ে কেউ নেই বাড়িতে? তার হাত দিয়ে… বুঝলি এখন?’
গাড়োয়ান একটু কী যেন ভাবিল, তাহার পর বলিল, ‘পারব হুজুর। দেন!’
জাহাঙ্গীর চিঠিটা ও দশ টাকার নোট তাহার হাতে দিয়া বলিল, ‘কাল সন্ধ্যায় আমায় এইখানে পাবি এসে। কী উত্তর দেয়, নিয়ে আসবি। তা হলে আরও দশ টাকা বকশিশ, বুঝলি?’
গাড়োয়ান আনন্দ-গদগদ কণ্ঠে বলিল, ‘হুজুর মা বাপ! কালই সনঝেবেলা আমি হাজির হব এসে। হুজুর এইখেনেই থাকবেন তো?’
জাহাঙ্গীর ‘হুঁ’ বলিয়া অন্যমনস্কভাবে স্টেশনের ভিতরে চলিয়া গেল।
ওয়েটিং রুমে ঢুকিয়াই সে একেবারে চমকিয়া উঠিল। সেখানে ইজিচেয়ারে শুইয়া সাহেবি পোশাকপরা এক জন লোক নিশ্চিন্ত আরামে সিগার ফুঁকিতেছিল। জাহাঙ্গীর লোকটিকে আর একবার ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিল, তাহার পর কাছে গিয়া বলিল, ‘প্রমতদা এখানে?’
প্রমত্তও চমকিয়া উঠিয়াছিল। জাহাঙ্গীরকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল, ‘চুপ! এখানে প্রমতদা বলে কেউ আসেনি!’ বলিয়াই চতুর্দিকে সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, ‘বস এইখানে। তার পর তুই এখানে কোথা?’
জাহাঙ্গীর সমস্ত বলিল।
প্রমত্ত সমস্ত শুনিয়া হাসিয়া বলিল, ‘বেশ বেড়াচ্ছিস তা হলে উপন্যাসের নায়ক হয়ে! কিন্তু ভালো করিসনি জাহাঙ্গীর তুই এখানে এসে। যাক, তুই আজই কোলকাতা চলে যা। একটু পরেই ট্রেন আসবে!’
জাহাঙ্গীর বিস্মিত হইয়া বলিল, ‘আর আপনি?’
প্রমত্ত বলিল, ‘আবার প্রশ্ন? আমার অন্য জায়গায় কাজ আছে।’
কী যে কাজ জাহাঙ্গীরের তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না। ইহা লইয়া আর কিছু প্রশ্ন যে সে করিতে পারে না, তাহাও সে জানে। তবু সে একটু ঘুরাইয়া বলিল, ‘আমাকে যে কাল পর্যন্ত থাকতে হচ্ছে প্রমতদা!’ বলিয়াই সে হাসিয়া বলিল, ‘থুড়ি, মিস্টার চাকলাদার!’
প্রমত্ত হাসিয়া বলিল, ‘আমার সুটকেসের লেখা নাম পড়ে ফেলেছিস বুঝি? কিন্তু দেয়ালগুলোরও চোখকান আছে রে! একটু সাবধানে কথাবার্তা বলবি। সে যাক, তুই এখানে থাকবি কেন, বল তো! আমার জন্য তোর কোনো চিন্তা নেই।’
জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, ‘আপনার নেই, কিন্তু আমাদের তো থাকা উচিত। তা ছাড়া’ – বলিয়াই একটু থামিয়া চক্ষু নত করিয়া বলিল, ‘কাল চিঠির উত্তর আসবে আমার!’
প্রমত্ত হাসিল না। জাহাঙ্গীরের দিকে তাকাইয়া অনেকক্ষণ কী ভাবিল। তাহার পর আস্তে আস্তে বলিল, ‘তবে তুই থাক। কিন্তু খুব সাবধান। পিছনে টিকটিকি লেগেছে! অবশ্য, তোর ভাবনা নেই। কেননা মুসলমান যুবককে তারা এখনও সন্দেহ করেনি। সাবধানের মার নেই।’
প্রমত্ত আবার যেন কী ভাবিতে লাগিল।
একটু পরে সে বলিয়া উঠিল, ‘দেখ জাহাঙ্গীর, তোর আচকান পায়জামা আছে সঙ্গে?’
জাহাঙ্গীর বলিল, ‘আছে।’
প্রমত্ত বলিল, ‘এক্ষুনি নিয়ে আয়!’ বলিয়াই ঘড়ির দিকে তাকাইয়া বলিল, ‘আর বেশি সময় নেই! যা, শিগগির আন!’
জাহাঙ্গীর তাহার আচকান পায়জামা আনিলে প্রমত্ত বাথরুমে ঢুকিয়া একটু পরে যখন তাহা পরিয়া বাহির হইয়া আসিল, তখন জাহাঙ্গীর একটু জোরে হাসিয়া বলিল, ‘আদাব আরজ মউলবি সাব! আপকে ইসমে শরিফ!’
প্রমত্ত হাসিয়া বলিল, ‘কেফায়েতুল্লা।’ তার পর নিম্নকন্ঠে বলিল, ‘আমি যাচ্ছি এখনই! কেমন যেন গন্ধ পাচ্ছি রে! তুই এইখানেই ঘুমো। দরকার হলে ডাকব!’ বলিয়াই প্রমত্ত টার্কি-ফেজ মাথায় দিয়া ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাহির হইয়া গেল!
জাহাঙ্গীর সেইখানে ইজিচেয়ারে শুইয়া শুইয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িল।
রাত্রি প্রায় তিনটার সময় সে কাহার ঠেলায় জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, সামনেই একজন ইউরোপিয়ান সাহেব। তাহার পিছনে তিন-চার জন বাঙালি বাবু।
সে একটু বিরক্ত হইয়াই ইংরাজিতে বলিল, ‘আপনি কী চান? এরূপভাবে জাগাবার রীতি ভদ্রতা-বিরুদ্ধ!’
সাহেব একটু থতমত খাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিল, ‘মাপ করবেন, আমি আপনাকে আমার বন্ধু মি. চাকলাদার মনে করেছিলুম। তিনি বোধ হয় এখানেই ছিলেন, বলতে পারেন , তিনি কোথায় গেছেন?’
জাহাঙ্গীর তেমনি বিরক্তির সুরে বলিল, ‘জানি না কে আপনার চাকলাদার! আমি কাউকেই দেখিনি এখানে।’
সাহেব আবার ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া চলিয়া গেল।
জাহাঙ্গীরের বুঝিতে বাকি রহিল না ইনি কোন সাহেব!
এক অজানা আশঙ্কায় তাহার বুক কাঁপিতে লাগিল। সে আর একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিল, তাহার বুকের কাছে তাহার শ্রেষ্ঠ বন্ধু – তাহার আত্মরক্ষার অস্ত্র আছে কি না।
প্রমত্তকে সে জানিত। সে জানে, ইহাদের চক্ষে ধুলা দিতে এক জাহাঙ্গীরই যথেষ্ট, প্রমত্তের ন্যায় সেনানীর দরকার পড়ে না। তবু তাহার কেমন যেন ভয় করিতে লাগিল!
হঠাৎ অন্য দ্বার দিয়া ঢুকিয়া প্রমত্ত বলিয়া উঠিল ‘আসসালামো আলায়কুম! ক্যা মিয়াঁসাব শ্বশরুয়া চলা গিয়া?’
জাহাঙ্গীর লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, ‘জি হাঁ! মগর আপ ইস ওক্ত ক্যেঁও’ – বলিয়াই এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করিয়া গলা খাটো করিয়া বলিল, ‘আপনি সরে পড়ুন প্রমতদা, স্যাঙাতরা নিশ্চয় এইখানেই কোথাও আছে!’
প্রমত্ত পরম নিশ্চিন্তভাবে চেয়ারে বসিয়া বলিল, ‘তোকে সে ভাবনা ভাবতে হবে না। তুই চল দেখি আমার সাথে, এখখুনি এক জায়গায় যেতে হবে।’
জাহাঙ্গীর কোনো প্রশ্ন না করিয়া মিলিটারি কায়দায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল ‘রেডি স্যার।’
সমস্ত জিনিসপত্র স্টেশন মাস্টারের হেফাজতে রাখিয়া সে বাহিরে আসিয়া দেখিল, একখানা মোটরের সম্মুখে প্রমত্ত সন্ন্যাসীর সাজে সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছে। দুইজনে মোটরে উঠিয়া বসিলে মোটর বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া চলিল।
জাহাঙ্গীর বলিল, ‘কী করতে হবে দাদা আমায়, জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?’
প্রমত্ত হাসিয়া বলিল, ‘আর কেউ হলে বলতাম না, আমি তোকে জানি বলেই বলছি। একটু দূরেই কোনো গ্রামে যাচ্ছি। সেখানে আমাদের কিছু অস্ত্রশস্ত্র আছে। পুলিশ তা টের পেয়েছে বলে খবর পেয়েছি। আজ ভোরের মধ্যেই তা সরিয়ে আর কোথাও রেখে যেতে হবে – আমার ওপর বজ্রপাণির এ হুকুম।’
জাহাঙ্গীর কিছু প্রশ্ন করিল না। উত্তেজনা উৎসাহে তাহার রক্ত গরম হইয়া উঠিল। হঠাৎ সে প্রশ্ন করিয়া বসিল, ‘রাস্তায় যদি পুলিশের সঙ্গে দেখা হয়?’
প্রমত্ত উত্তর দিল না। মাঝে মাঝে উঁকি দিয়া রাস্তার দিকে দেখিতে লাগিল। হঠাৎ এক জায়গায় গাড়ি থামাইতে বলিয়া একটি ক্ষুদ্র শিস দিল। দেখিতে দেখিতে অন্ধকার ভেদ করিয়া চার পাঁচজন লোক আসিয়া নিঃশব্দে মোটরে বসিতেই আবার মোটর ছুটিতে লাগিল।
ঘণ্টাখানেক পরে তাহারা একটি গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া বাঁশবন-ঘেরা একটি ক্ষুদ্র মেটে ঘরের সম্মুখে আসিয়া থামিল। জাহাঙ্গীর সেই স্বল্প তারকালোকেই দেখিতে পাইল, গাড়ি থামিবামাত্র একটি স্ত্রীলোক দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রমত্ত গিয়া তাঁহার পায়ের ধুলা লইল।
প্রমত্তের ইঙ্গিতে সকলে নামিয়া পড়িল এবং সকলের সাথে জাহাঙ্গীরও মহিলাটিকে প্রণাম করিল, কিন্তু সে যেন দায়ে পড়িয়া।
ঘরের ভিতরে গিয়া স্বল্প দীপালোকেই জাহাঙ্গীর যে মহীয়সী জ্যোতির্ময়ী মূর্তি দেখিল, তাহাতে এই নারীকে প্রণাম করিতে গিয়া তাহার মন যে-টুকু বিস্বাদ হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার জন্য নিজেকে ধিক্কার না দিয়া পারিল না।
মহিলার বয়স ছত্রিশ সাঁইত্রিশের বেশি হইবে না। পরনে শুধু একখানি পরিষ্কার সাদা ধুতি। যেন গায়ের রং-এর সাথে মিশিয়া গিয়াছে। ঘাড় পর্যন্ত ছোটো করিয়া কাটা চুল – অনেকটা বাবরি চুলের মতো। তাহারই কতকগুলো ললাটে ও মুখের আশেপাশে আসিয়া পড়িয়াছে। বড়ো বড়ো চক্ষু, কিন্তু তাহা যেন একটু অতিরিক্ত প্রখর, সহজে চোখের দিকে চাওয়া যায় না। চোখ যেন ঝলসিয়া যায়। মুখ পুরুষের মতো দৃপ্ত, মহিমোজ্জ্বল!
জাহাঙ্গীর মনে মনে বলিল, ‘নারী যদি নাগিনি হয়, তুমি নাগেশ্বরী।’
জাহাঙ্গীরের চিন্তায় বাধা পড়িল। প্রমত্ত নিম্নস্বরে বলিল, ‘এদের সব কে বুঝি চেন না জয়তীদি?’
জাহাঙ্গীর মনে মনে বলিল, ‘তুমি সত্যই জয়তী দেবী।’ জীবনে সে বুঝি এই প্রথম নারীকে শ্রদ্ধার চোখে দেখিল। জয়তী দেবী সকলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে জাহাঙ্গীর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, ‘এ ছেলেটিকে তো আগে দেখিনি!’
প্রমত্ত হাসিয়া বলিল, ‘এ পথ-ভোলা ছেলে দিদি। এ আমাদের গোষ্ঠীর নয়।’
প্রমত্তের এই কথায় অন্যান্য সকলে চঞ্চল হইয়া উঠিল। শুধু জয়তী দেবী বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে জাহাঙ্গীরকে দেখিতে লাগিলেন! হঠাৎ তিনি প্রশ্ন করিয়া বসিলেন ‘তোমার মা বেঁচে আছেন?’
জাহাঙ্গীর উত্তর করিল, ‘আছেন।’ জয়তী যেন আরও আশ্চর্য হইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিলেন।
প্রমত্ত হাসিয়া বলিল, ‘দিদি বোধ হয় ভাবছ, মা থাকতে ওর অমন লক্ষ্মীছাড়ার মতো চেহারা কেন, না? সত্যিই ও লক্ষ্মীছাড়া। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে পেরেছে বলেই ওকে দলে নিয়েছি।’
জয়তীর প্রখর চক্ষু স্নেহে কোমল হইয়া আসিল। স্নেহসিক্ত কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, ‘তুমি আমায় দিদি না বলে মাসিমা বলে ডেকো, কেমন?’ বলিয়াই জয়তী অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন।
জাহাঙ্গীর ব্যতীত আর সকলেরই চক্ষু জলে পুরিয়া উঠিল! জয়তীর এই অনুরোধের অর্থ বুঝিতে তাহাদের বাকি রহিল না।
জয়তীর ছোটো বোন সন্তান-প্রসব করিয়াই মারা যায়। সেই ছেলেকে জয়তী লইয়া আসিয়া মানুষ করেন। নাম রাখেন পিনাকপাণি। সকলে ‘পিনাকী’ বলিয়া ডাকিত। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া গত বৎসর তাহার ফাঁসি হইয়া গিয়াছে! ফাঁসির মঞ্চেও সে জীবনের জয়গান গাহিয়াছে!
যেদিন পিনাকীর ফাঁসি হয়, সেইদিনই জয়তী গঙ্গাস্নান করিয়া রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া স্বয়ং বজ্রপাণির কাছে স্বদেশি মন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেন। আজ জয়তী বিপ্লবীদের শক্তি-স্বরুপা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন।
জয়তীর ওই উক্তির পর সকলে এমনকি প্রমত্ত পর্যন্ত বিস্মিত হইয়া দেখিল, জাহাঙ্গীরের সঙ্গে পিনাকীর বেশ খানিকটা সাদৃশ্য আছে।
পিনাকীকে বিপ্লব-সংঘে সকলেই অতিরিক্ত স্নেহ করিত। সে ছিল তাহাদের দলের বয়োকনিষ্ঠদের অন্যতম। তাহা ছাড়া, সে যাইত সর্বাপেক্ষা দুঃসাহসের কাজে সর্বাগ্রে।
মৃত্যুকে সে রাঙা উত্তরীয়ের মতো সারা গায়ে জড়াইয়া ধরিতে চাহিত!
তাহার ফাঁসির দিন বজ্রপাণি হইতে আরম্ভ করিয়া বিপ্লবীদের প্রত্যেকে শিশুর মতো রোদন করিয়াছিল।
ফাঁসির পূর্বে ম্যাজিস্ট্রেট যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, ‘তুমি কি কাউকে দেখতে চাও?’
পিনাকী হাসিয়া বলিয়াছিল, ‘চাই, কিন্তু তুমি তা দেখাতে পারবে না!’
ম্যাজিস্ট্রেট তার শিশুর মতো মুখের পানে তাকাইয়া জোরের সঙ্গে বলিয়াছিল, ‘নিশ্চয়ই পারব! বলো কাকে দেখতে চাও?’
পিনাকী তেমনি মধুর হাসিতে মুখ আলো করিয়া বলিয়াছিল, ‘আমি চাই ভারতের স্বাধীনতা দেখতে! পারবে দেখাতে?’
ম্যাজিস্ট্রেট তৎক্ষণাৎ তাহার মাথার টুপি খুলিয়া বালককে অভিবাদন করিয়া অশ্রুপূর্ণনেত্রে বলিয়াছিল, ‘আমি তোমায় প্রণাম করি বালক। মৃত্যুমঞ্চই তোমার মতো বীরের মৃত্যুঞ্জয়ী সম্মান। তোমার মতো বীরের বন্দনা করবার সম্বল জীবনের নাই।’
আজ জয়তী দেবীর জাহাঙ্গীরের প্রতি এই অদ্ভুত অনুরোধ শুনিয়া সকলের সেই সব কথাই স্মরণ হইতে লাগিল!
একটু পরেই জয়তী আসিয়া বলিলেন, ‘তোমরা তোমাদের কাজ করো গিয়ে, আমি একটু ওর সঙ্গে আলাপ করি।’
প্রমত্ত অন্যান্য ছেলেদের লইয়া চলিয়া গেল। জাহাঙ্গীর একা কেমন একটু অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল।
জয়তী কাছে আসিয়া বসিয়া বলিলেন, ‘তোমায় পিনাকী বলে ডাকব, কেমন?’ –কণ্ঠ তাঁর যেন ভাঙিয়া আসিল।
জাহাঙ্গীরের চক্ষে এতক্ষণে যেন এই রহস্যের কুহেলিকা কাটিয়া গেল। এখন সে বুঝিতে পারিল, কেন জয়তী দেবী তাহাকে মাসিমা বলিতে অনুরোধ করিলেন। তাহারও চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে তাহার দুই চক্ষু বহিয়া টসটস করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। হঠাৎ সে বলিল, ‘তুমি কি বীর পিনাকীর মাসিমা?’
জাহাঙ্গীরের এই তুমি সম্ভাষণে এমন পাষাণ-প্রতিমার মতো কঠিন জয়তীও যেন ভাঙিয়া পড়িলেন। জাহাঙ্গীরের শিরশ্চুম্বন করিয়া বলিলেন, ‘হাঁ বাবা ‘আমিই সে দুর্ভাগিনি।’
তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন, ‘তোকে দেখতে অনেকটা পিনাকীর মতো।’
জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, ‘তুমি দুর্ভাগিনি নও মাসিমা, ভাগ্যবতী। কিন্তু সে যাক, তোমায় না ভেবে ছুঁয়ে ফেলেছি, তোমায় হয়তো আবার স্নান করতে হবে!’
জয়তী বেদনায় নীল হইয়া বলিলেন, ‘ও কথা বলিসনে বাবা, ও কথা শুনলেও পাপ হয় মানুষকে মানুষ ছুঁলে স্নান করতে হয়, মানুষের এত বড়ো অবমাননাকর শাস্ত্র সৃষ্টি হয়েছিল বলেই আমাদের এই দুর্দশা। জানিনে তুই কী জাত, কিন্তু তুই যদি হাড়ি-ডোমও হতিস তা হলেও তোকে ছুঁতে এতটুকু ইতস্তত হত না আমার! ওরে, জন্মটা তো দৈব। যেদিন আরেকজনকে আরেকজাতের ভেবে ঘৃণা করব, সেই দিনই আমার স্বাধীনতা মন্ত্র আমার কাছে ব্যর্থ হয়ে যাবে! তা ছাড়া, তোরা তো আগুনের শিখা, তোদের ছোঁয়ায় সেসব অশুচি শুচি হয়ে ওঠে বাবা!’
জাহাঙ্গীর অবাক হইয়া জয়তীর মুখের পানে তাকাইয়া বলিল, ‘এই যদি আমাদের অন্তরের কথা হয় মাসিমা, তা হলে এই আমাদের সবচেয়ে বড়ো মন্ত্র। আর শুধু এই মন্ত্রের জোরেই বিনা রক্তপাতে আমরা ভারত স্বাধীন করতে পারব।’
এমন সময় অন্য ঘর হইতে জয়তীর একমাত্র কন্যা ঘুম হইতে জাগিয়া ‘মা মা’ বলিয়া ডাকিতে লাগিল।
জয়তী কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, ‘এইখানে উঠে আয় চম্পা, তোর একজন নতুন দাদা এসেছে।’
চম্পা আলুথালু বেশে তাহার মাতার নিকট আসিয়া বলিল, ‘কই মা?’ বলিয়াই জাহাঙ্গীরকে দেখিয়া একটু থতমত খাইয়া গেল।
জয়তী মলিন হাসি হাসিয়া বলিলেন, ‘ওকে অনেকটা পিনাকীর মতো দেখাচ্ছে, না?’
পিনাকীর নাম করিতেই চম্পার দুই চোখে অশ্রুর বান ডাকিল। সে সেই অশ্রুসিক্ত চক্ষু দিয়া জাহাঙ্গীরকে দেখিতে দিখিতে হঠাৎ তাহার কাছে আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল, ‘দাদাকে কী বলে ডাকব মা?’
জয়তী হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, ‘দাদাকে আবার কী বলে ডাকবি? দাদাই বলবি!’
চম্পা লজ্জা পাইয়া জয়তীর পশ্চাতে আসিয়া মুখ লুকাইল!
জাহাঙ্গীর দেখিল, চম্পা যেন শুক্লা চতুর্দশীর চাঁদ। সহসা তাহার ভূণীকে মনে পড়িল। ইহারা মায়াবিনীর জাত। ইহারা সকল কল্যাণের পথে মায়াজাল পাতিয়া রাখিয়াছে। ইহারা সকল কল্যাণের পথে মায়াজাল পাতিয়া রাখিয়াছে। ইহারা গহনপথের কণ্টক, রাজপথের দস্যু। সে নিঃশব্দে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। দেখিল, দূরে বনানীর অন্ধকারে নিশীথের চাঁদ মলিনমুখে অস্ত যাইতেছে, আর পূর্বগগন নবারুণের উদয় আশায় রাঙিয়া উঠিতেছে!
কুহেলিকা – ১২
জাহাঙ্গীর কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়াই দেখে দুই তিনখানা টেলিগ্রাম আসিয়া পড়িয়া আছে। একখানা দেওয়ানজির, দুইখানা তাহার মায়ের প্রেরিত। পর পর দুইখানা টেলিগ্রাম করিয়াও তাহার উত্তর না পাইয়া স্নেহবৎসলা জননী আবার ‘রিপ্লাই-পেড’ টেলিগ্রাম করিয়াছেন। এইবার উত্তর না দিলে দেওয়ানজিকে লইয়া তিনি নিজেই কলিকাতা আসিয়া তাহাকে পাকড়াও করিবেন – এমন ইঙ্গিতও দিয়াছেন টেলিগ্রামে।
জাহাঙ্গীরের মাতা ঘুণাক্ষরেও জানিতেন না যে তাঁহার পুত্র বিপ্লব-মন্ত্রে দীক্ষা লইয়াছে, বা সে কলিকাতায় মাঝে মাঝে থাকে না – ওই মন্ত্রের উপাসনার জন্য। কাজেই তিনি মনে করিতেছিলেন, হয় জাহাঙ্গীর পীড়িত, নয় সে ইচ্ছা করিয়াই উত্তর দিতেছে না।
জাহাঙ্গীর ভয়ে ভয়ে শেষ টেলিগ্রামের তারিখ দেখিয়া বুঝিল, ও টেলিগ্রামও দুই দিন আগেকার। সে সর্বাপেক্ষা অধিক বিস্মিত হইল, টেলিগ্রাম খোলা দেখিয়া। অনেক অনুসন্ধান করিয়াও সে জানিতে পারিল না, কে তাহার টেলিগ্রাম খুলিয়াছে। শেষে তাহার বুঝিতেও বাকি রহিল না, এ কীর্তি কাহাদের। সে শ্রান্তভাবে ধূলি-ধূসরিত বিছানায় শুইয়া পড়িয়া সিগারেট ফুঁকিতে ফুঁকিতে গলা-ছাড়িয়া গান ধরিয়া দিল, ‘নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে!’
তখন কুম্ভীর মিয়াঁ ছাড়া আর প্রায় সকলেই আপন আপন কাজে বা কলেজে চলিয়া গিয়াছে। কাজেই কেহ আসিয়া আর জাহাঙ্গীরের অনুপস্থিতি লইয়া প্রশ্ন করিয়া বিব্রত করিল না।
আসিল কেবল কুম্ভীর মিয়াঁ তাহার ভুঁড়ি আন্দোলিত করিতে করিতে। কিন্তু সে ঘরে ঢুকিয়া জাহাঙ্গীরের মূর্তি দেখিয়া ভয় পাইয়া গেল। জাহাঙ্গীরের এমন ছন্নছাড়া মূর্তি সে যেন আর কখনও দেখেনি। দুঃখে, বেদনায়, বিস্ময়ে সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।
জাহাঙ্গীর বুঝিতে পারিয়া গম্ভীরভাবে কুম্ভীর মিয়াঁর ভুঁড়িতে তাকিয়া থাপড়ানোর মতো করিয়া থাপ্পড় মারিয়া বলিয়া উঠিল, ‘আমি উলঝলুল! দেখছিস কী হাঁ করে? আমি কি তোর বউ-এর ছোটো বোন?’ – বলিয়াই সিগারেট-কেস আগাইয়া দিয়া হুস করিয়া তাহার মুখের উপর একরাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া দিল।
অন্য দিন হইলে কুম্ভীর মিয়াঁ ছাড়িয়া কথা বলিত না। কিন্তু আজ সে সমস্ত অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া গেল। সে কত কথা জিজ্ঞাসা করিবে, কত কথা জানাইবে বলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল, কিন্তু সব যেন তাহার ঘুলাইয়া গেল জাহাঙ্গীরের এই চেহারা দেখিয়া। জাহাঙ্গীরকে সে এতদিন ধরিয়া দেখিতেছে, তবু সে যেন বিস্ময়ের দেশের রাজকুমার মায়াবী। উহাকে শুধু দেখিতে হয়, বুঝিবার চেষ্টা করা বৃথা। অথবা সে উন্মাদ।
ভাবিতে ভাবিতে সে নীরবে সিগারেট ধরাইয়া টানিতে লাগিল। জাহাঙ্গীরও কোনো কথা জিজ্ঞাসা করিল না। ঘুমে তখন তাহার চক্ষু যেন জড়াইয়া আসিতেছে। পুলিশের চক্ষে ধুলা দিবার জন্য আজ তিন দিন তিন রাত্রি তাহার নিজের চক্ষুকে নিস্তন্দ্র নির্ঘুম করিয়া রাখিতে হইয়াছে। সে জানিত, সে এতটুকু অবহেলা করিলে তাহার সহিত আরও বহু যুবকের জীবন বিপন্ন হইয়া পড়িবে। সে ক্ষণে ক্ষণে নানা রূপের আড়ালে নিজেকে লুকাইয়া বেড়াইয়াছে। কিন্তু আজ আর যেন সে পারে না।
সবচেয়ে বেশি ভয় হইতে লাগিল তাহার মাতার টেলিগ্রাম দেখিয়া। যদি তিনি কলিকাতায় আসিয়া পড়েন। কিন্তু কেন যে তাহাকে কুমিল্লা যাইবার জন্য এত অনুরোধ, তাহাও সে বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার মা তো জানেন, জমিদারি সংক্রান্ত ব্যাপারে সে হস্তক্ষেপ করিতে নারাজ এবং অপারগ – দুই-ই।
কুম্ভীর মিয়াঁ এক নিশ্বাসে তিন-তিনটা সিগারেটের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনপূর্বক হঠাৎ বলিয়া উঠিল, ‘এই! চা খাবি?’
জাহাঙ্গীর লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, ‘দে না ভাই লক্ষ্মীটি।’ বলিয়াই কুম্ভীর মিয়াঁর দাড়িতে হাত বুলাইয়া চুমু খাইল।
কুম্ভীর মিয়াঁ ম্লান হাসি হাসিয়া চলিয়া গেল। একটু পরে চা লইয়া আসিয়া দেখিল, জাহাঙ্গীর শেভ করিতে বসিয়া গিয়াছে।
এক পাশের আধ-কামানো গাল লইয়া জাহাঙ্গীর চায়ের কাপ টানিয়া লইল। চা খাইতে খাইতে বলিল, ‘দেখেছিস মুখের অবস্থা? আজ সাত দিন ক্ষৌরী না করে মুখ যেন ধান-কাটা মাঠের মতো হয়ে উঠেছে!’ বলিয়াই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, ‘হাত বুলোতে মনে হচ্ছিল, যেন কাটা-ধানের নাড়ার ওপর দিয়ে বাবলা গাছ টেনে নিয়ে যাচ্ছে!’ – আবার সেই হাসি!
কুম্ভীর মিয়াঁ এতক্ষণে যেন একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিয়া বলিল, ‘উঃ, এতক্ষণে যেন মেঘ কাটল! ভাগ্যিস চায়ের সৃষ্টি হয়েছিল, নইলে এমন বিপদে বিপদহন্ত্রীর বেশে আর কে দেখা দিত!’ – বলিয়ায় রাস্তার কাঁসারির কংসনিনাদের মতো বাজখাঁই হাসি!
জাহাঙ্গীরও সে হাসিতে হাসিতে যোগদান করিয়া বলিল, ‘যা বলাছিস! চা আর সিগারেট–যেন একসঙ্গে বউ আর শালি!–আঃ কী চা-ই করেছিস! তোর শালির বিয়েচে আমি চালনি দিয়ে জল বয়ে দিব!’ কুম্ভীর মিয়াঁ জাহাঙ্গীরের ঊরুতে এক রাম-থাপ্পড় কষাইয়া বলিয়া উঠিল, ‘তুই কী এমনই সতী!’
জাহাঙ্গীর ঊরুতে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল, ‘তুই ভীম হতে পারিস, তাই বলে আমি দুর্যোধন নই! এখনই ঊরুভঙ্গ হয়েছিল আর কী!’
কুম্ভীর মিয়াঁ এতক্ষণে যেন কূল পাইয়া বলিয়া উঠিল, ‘আচ্ছা দুর্যোধনের মতো কোন হ্রদে লুকিয়েছিলি বল তো?’
জাহাঙ্গীর কোনো উত্তর দিল না। চা শেষ করিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে দাড়ি কামাইতে লাগিল।
কুম্ভীর মিঁয়া বলিয়া উঠিল, ‘আরে তোমায় খবর দিতে ভুলে গেছি, তোমাদের দেওয়ানজি এসেছেন যে!’
জাহাঙ্গীর চমকিয়া উঠিতেই খানিকটা গাল কাটিয়া গেল। ক্ষতস্থানটা চাপিয়া ধরিয়া জাহাঙ্গীর বলিয়া উঠিল, ‘কোথায় তিনি? কখন এসেছেন?’
কুম্ভীর মিঁয়া বিস্মিতনেত্রে জাহাঙ্গীরের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, ‘তা তো জানিনে। তবে তিনি কাল দু-তিনবার এসেছিলেন তোমার খোঁজ করতে। আজও সকালে একবার এসেছিলেন যেন। যাক, তোর চিন্তার কিছু নেই। তিনি নিজেই আজ আর একবার অন্তত আসবেন।’
জাহাঙ্গীর কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া গেল, এবং একটু চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া নিঃশব্দে দাড়ি কামাইয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল। স্নান করিয়া ফিরিয়া সে শুইয়া পড়িয়া বলিল , ‘আমি এখন একটু ঘুমুব! শরীরটা কেমন খারাপ করছে যেন। দেওয়ানজি এলে আমায় উঠিয়ে দিস।’
জাহাঙ্গীরের যখন ঘুম ভাঙিল, তখন বেলা গড়াইয়া পড়িয়াছে। ঘুম ভাঙিতেই দেখিল সামনে চেয়ারে বসিয়া দেওয়ানজি। জাহাঙ্গীর উঠিয়া শশব্যস্তে তাঁহার পায়ের ধুলা লইল।
দেওয়ানজি তাহাকে একেবারে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিলেন, ‘বাবা, বেগম মা অস্থির হয়ে উঠেছেন। তুমি এখনই চলো। আজ দু-দিন তিনি না খেয়ে আছেন।’
জাহাঙ্গীর কুঁজো হইতে জল গড়াইয়া লইয়া চোখে মুখে দিতে দিতে বিস্ময়ান্বিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ‘মা? মাও এসেছেন নাকি?’
দেওয়ানজি বলিলেন, ‘হাঁ বাবা, তোমার কোনো খবর না পেয়ে অসুখ-বিসুখ হয়ছে মনে করে কাল আমরা এসেছি। এসে অবধি তোমায় খুঁজছি। তুমি সাত দিন ধরে এখানে নেই শুনে তিনি সেই যে শয্যা নিয়েছেন আর ওঠেননি। কেউ এতটুকু পানি মুখে দিতে পারেনি!’
জাহাঙ্গীর জামা পরিতে পরিতে ক্লান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, ‘কোন বাড়িতে উঠেছেন এসে?’
দেওয়ানজি উঠিতে উঠিতে বলিলেন, ‘লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়িতে। অন্য বাড়ি তো সব ভাড়া দেওয়া হয়ে গেছে। ওটাই শুধু খালি হয়েছে মাত্র সেদিন!’- বলিয়াই একটু থামিয়া বলিয়া উঠিলেন, ‘তুমি তো কোনো খবরই রাখ না বাবা। নিজের বাড়িঘরগুলোরও না।’
জাহাঙ্গীর উচ্চবাচ্য না করিয়া বাহির হইয়া পড়িল।
দেওয়ানজি নামিতে নামিতে দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, ‘কী চেহারা হয়েছে তোমার, দেখো তো! কে বলবে নওয়াব বাড়ির ছেলে! যেন পথের ভিখিরি!’
জাহাঙ্গীর হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, ‘আমি তো সত্যই ভিখিরি দেওয়ান সাহেব! বাপের জমিদারি, ও তো আমি অর্জন করিনি!’
জাহাঙ্গীরের চোখে-মুখে এক অব্যক্ত-ব্যথার ছাপ ফুটিয়া উঠিল। দেওয়ানজি কিছু বুঝিতে না পারিয়া বিমূঢ়ের মতো তাকাইয়া থাকিলেন।
মোটরে যাইতে যাইতে জাহাঙ্গীর সাহস পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘আচ্ছা দেওয়ান সাহেব, খবর সব ভালো তো? এত ঘন ঘন টেলিগ্রাম করা কেন বলুন তো! এ অকর্মণ্যকে নিয়ে কেন এ অনর্থক টানাটানি?’– তাহার কথায় সুরে তিক্ত শ্রান্তি ফুটিয়া উঠিল।
দেওয়ানজি স্টেট চালাইয়া ঝানু হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু মানুষের বিশেষ করিয়া আজকালকার যুবকদের অন্তর লইয়া কখনও তাঁহার মাথাব্যথা হয়ও নাই, আর চেষ্টা করিয়াও ওর কূল পান না। তবু তাঁহার হঠাৎ মনে হইল তরুণ যুবক হয়তো-বা কোথাও লভ-টভ করিয়া বসিয়াছে। তিনি মনে মনে এ রোগের ওষুধের কথা চিন্তা করিয়া প্রসন্ন হইয়া উঠিলেন।
বলিয়া উঠিলেন, ‘খবর ভালোই বাবা। শুধু আমাদের বেগম-মা জিদ ধরেছেন, তিনি মক্কা যাবেন হজ করতে। আর এক হপ্তার মধ্যেই জাহাজ ছাড়বে। তিনি তোমায় সমস্ত বুঝিয়ে দিয়ে যেতে চান । তাই এত তাড়াতাড়ি!’
জাহাঙ্গীর আর শুনিতে পারিল না। কেমন যেন এক অজানা আতঙ্কে তাহার সারা দেহ মন শিহরিয়া উঠিল। অসহায়ভাবে মোটরে হেলান দিয়া শুইয়া পড়িয়া বলিল, ‘দেওয়ান সাহেব, এখন থাক, মার কাছে গিয়েই সব শুনব!’
কুহেলিকা – ১৩
জাহাঙ্গীর আসিয়া পৌঁছাইতেই তাহার মাতা একেবারে তাহাকে বুকে জড়াইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন, ‘খোকা, এ কী চেহারা হয়েছে তোর?’
জাহাঙ্গীর কিছু না বলিয়া মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। জননী উদ্গত অশ্রু সংবরণ করিতে করিতে নীরবে ছেলের মাথায় মুখে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।
জাহাঙ্গীর হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া বলিল, ‘তোমার খাওয়া হয়নি দু-দিন থেকে! আগে খেয়ে নাও, তার পর সব কথা হবে।’
অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুত্রের পীড়াপীড়িতে তাঁহাকে উঠিয়া খাইয়া আসিতে হইল।
জাহাঙ্গীর ততক্ষণে ঘরের চতুর্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল, সত্যসত্যই কোনো দূরদেশে যাইবার জন্যই তাহার মা প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। বুঝিতে তাহার বাকি রহিল না, মায়ের এ অভিমান কাহার উপর! সে সংসারী হইল না, ঘর সংসারের কোনোকিছু দেখিল না শুনিল না বলিয়াই মা স্বেচ্ছায় সংসার হইতে সরিয়া দাঁড়াইতেছেন। এ হয়তো অভিমান করিয়া পুত্রকে শাস্তিই দিতেছেন তিনি। জাহাঙ্গীর গভীর দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া একটা সোফায় বসিয়া অস্ত-আকাশের রং-এর খেলা দেখিতে লাগিল। রং তো নয়, ও মায়া, স্বপ্ন। ও রং লাগিতেও যতক্ষণ মুছিতেও ততক্ষণ।
ওই গোধূলিবেলার রং-এর মতো সুখের স্বপ্নের ছোপ তাহার চিত্তে লাগিয়াই আবার পরক্ষণে মুছিয়া যায়। ওই অস্ত-আকাশের মতোই নির্লিপ্ত তার মন। কত রং আসে, খেলিয়া যায়, তার পরে একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া যায় কঠোর বাস্তবের দিবালোকে। এই রং-এর মায়ায় সে ভুলিবে না। ইহাকে প্রশ্রয় দিবে না। তাহার কাছে শুধু দিনের আলো আর রাতের আঁধারই সত্য। নিষ্ঠুর বাস্তবতা আর অসীম দুঃখ সূর্যালোক আর আঁধারের মতো তাহার জীবনকে জড়াইয়া আছে। ইহাকে অতিক্রম করিয়া যাহা কিছু তাহা কেবলই রং-এর মায়া, মরীচিকার প্রতারণা।
সে কী করিবে ভাবিতে লাগিল।
কিন্তু বেশি ভাবিবার অবকাশও সে পাইল না। মাতা খাইয়া আসিয়া পার্শ্বে বসিয়া বলিলেন, ‘সত্য বল দেখি খোকা, তোর কী হয়েছে! দিন দিন তোর চেহারাই বা অমন হচ্ছে কেন? কী হয়েছিস, একবার আয়নার দিকে তাকিয়ে দেখ দেখি।’
জাহাঙ্গীরের মেসে বড়ো আয়না ছিল না। তাছাড়া চুলটুল চিরুনিও করে সে সাধারণত কম। করিলেও এত অন্যমনস্কভাবে করে, যে তাহার নিজের চেহারার দিকে লক্ষ করিবার মতো মনের অবস্থা তাহার থাকে না। মায়ের কথায় হঠাৎ সামনের বড়ো আয়নার দিকে তাকাইয়া সে নিজেকে এতদিন পরে ভালো করিয়া দেখিল। দেখিয়া লজ্জিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। সত্যই তাহার চেহারা অতিমাত্রায় লক্ষ্মীছাড়া হইয়া গিয়াছে। এই ঘরে তাহাকে যেন মানাইতেছিল না।
তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, রাজবাড়িতে ভিক্ষুককে যেমন অশোভন দেখায়, তাহাকে তেমনই বিশ্রী বেখাপ্পা দেখাইতেছে। সে মনে মনে সংকুচিত হইয়া উঠিতে লাগিল!
সে জানে, রাজ-ঐশ্বর্য এই ঘরবাড়ি ধনদৌলত সমস্ত তাহারই একদিন হইবে। অথবা ইচ্ছা করিলে আজই সে এসবের মালিক হইতে পারে। তবু তাহার মন কেন যেন কেবলই বলিতে লাগিল, এ ঐশ্বর্য আর কারুর, তোর নয়, তোর নয়! কেন যেন তাহার মন এত বড়ো অধিকার, এত বেশি ঐশ্বর্যকে স্বীকার করিয়া লইতে পারে না, তাহা সে নিজেই জানে না।
দেশের কাজে নিয়তই তাহাকে দুঃখী আতুরদের মাঝেই বেশিরভাগ ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছে। তাহাদের শত অপরাধের মাঝে থাকিয়াও তো সে এ অস্বস্তি অনুভব করে নাই। বরং পরম শান্তির সঙ্গে এই দুঃখের দৈন্যের বুকে বসিয়া সে ভাবিয়াছে, সে যেন এই দৈন্য-দুঃখপীড়িত দলেরই এক জন। ঐশ্বর্যের প্রলোভন মায়া তাহার জন্য নয়। সে ঐশ্বর্যকে ঘৃণা করে, ঐশ্বর্যশালীদের ঘৃণা করে। উহারাই সকল পাপের মূল। উহারাই শয়তানের গুপ্তচর। ওই ঐশ্বর্যই সকল অকল্যাণের হেতু।
তাহার জন্মবৃত্তান্ত আজ তাহার কাছে অবিদিত নাই। ইহা লইয়া প্রথমে যে চিত্তবিক্ষোভ হইয়াছিল, তাহাও অনেকটা আজ প্রশমিত হইয়া গিয়াছে – তাহার আত্ম-অবহেলায় আত্ম-নির্যাতনেও প্রমত্তের উপদেশ। তবু তাহার মনে হইতে লাগিল, আজ যদি আমার মা ওই দুঃখীদের মতোই এক জন হইত, সে আজ এমন করিয়া মাকে পর ভাবিতে পারিত না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এই বাহিরের ঐশ্বর্যই তাহার অন্তরের ঐশ্বর্যকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে। মনে মনে বলিল, দেবতার অভিশাপের মতোই দেবতার বরও ব্যর্থ হইবার নয়; সুতরাং এ বরের বর্বরতা যেদিন তাহার স্কন্ধে আসিয়া চড়িবে, সেদিন সে যেন তাহাকে পরিপূর্ণ চিত্তে অগাধ জলে বিসর্জন দিতে পারে।
এই সোনার লঙ্কাকে দগ্ধ করিতে পারে। বহু সীতার চোখের জলে এ লঙ্কা কলঙ্কিত।
বেদনাতুর আঁখি তুলিয়া মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘কী ভাবছিস খোকা অমন করে? কী হয়েছিস তুই? কেবলই কী যেন ভাবছিস! কথা কইছিস অন্যমনস্ক হয়ে। যেন অন্য বাড়ির ছেলে। আমার যে কত কথা আছে তোর সাথে!’
জাহাঙ্গীর ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, ‘বড্ড শরীরটা খারাপ লাগছে মা! আমি একটু শুই, শুয়ে শুয়ে সব কথা শুনব তোমার। তা ছাড়া পরীক্ষা কাছে কিনা, এবার পাশ করতে পারব কিনা ভাবছি।’
মাতা হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, ‘দেখ, মার মন অন্তর্যামী। আমার কাছে তোর আর লুকাতে হবে না। তোর মনের কথা না বলিস না-ই বললি, তবু এ লুকোবার চেষ্টা করিসনে। আর পরীক্ষায় ফেলের কথা? তুই তো চিরকাল না পড়েই পাশ করে এলি। আমি জানি, এবারও তুই পাশ করবি। কিন্তু তুই তো ও কথা ভাবছিসনে, অন্য কী কথা ভাবছিলি বল?’
জাহাঙ্গীর বিছানায় শুইয়া পড়িল, উপরের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিল।
একটু থামিয়া ধরা গলায় মা বলিয়া উঠিলেন, ‘খোকা আমি মা, আমি তোর মনের কথা যেন সব বুঝি। আচ্ছা বাবা, তোর কথায় আমি তো খেলুম, এখন তুই এ বাড়ির কিছু খাবি কি? তুই পেটের ছেলে, তবু যেন ও-অনুরোধটুকু করতেও আমার ভয় হয়!’– বলিতে বলিতে কান্নায় মাতার স্বর জড়িত হইয়া গেল!
জাহাঙ্গীরকে কে যেন চাবুক দিয়া আঘাত করিল। সে জ্যা-ছিন্ন ধনুকের মতো লাফাইয়া উঠিয়া মায়ের কোলে মাথা রাখিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, ‘মা! মা! তোমার পায়ে পড়ি, আর অমন করে বোলো না, আমিও আজ তিন দিন থেকে শুধু চা খেয়ে আছি। এতক্ষণ বলিনি। খাবার আনো, তুমি খাইয়ে দেবে!’
জাহাঙ্গীরকে বুকে জড়াইয়া ‘খোকা’ বলিয়া ডাকিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।
অনেকক্ষণ কাঁদিয়া চোখ মুছিয়া বলিলেন, ‘কী নিষ্ঠুর তুই খোকা, নিজে না খেয়ে আছিস তিন দিন, আর তা লুকিয়ে আমায় মাথার দিব্যি দিয়ে খাওয়ালি?’
জাহাঙ্গীর দুষ্টু ছেলের মতো আবদারের সুরে বলিয়া উঠিল, ‘বা রে, তুমি বুঝি জিজ্ঞাসা করেছিলে আমি খেয়েছি কিনা?’
চোখে আঁচল দিয়া মাতা চলিয়া গেলেন। পরিপাটি করিয়া ছেলেকে খাওয়াইবার পর মাতা বলিলেন, ‘তুই এখন শো দেখি। আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে সব কথা বলি।
জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, ‘আর সব কথা বলতে হবে না তোমার। আমি সব জানি। এরই মধ্যে হাজিবুড়ি হতে যাচ্ছ, এই তো!’
মাতা হাসিয়া বলিলেন, ‘তা বুড়ো তো হয়েছি বাবা। এইবার তোর জিনিস তুই নে। আমি আর যখের ধন আগলাতে পারিনে।’
জাহাঙ্গীরও তরল হাসি হাসিয়া বলিল, ‘অর্থাৎ যক্ষ ভূত হয়ে আমিই এ টাকাকড়ি নিয়ে পাহারা দিই! তা মা, জ্যান্ত ছেলেকেও যখ দেওয়া যায় না!’
মা ছেলের মুখ চাপিয়া বলিলেন, ‘তুই থাম খোকা। ষাট! বালাই! নিতে হবে না তোকে কিছু। দেওয়ান সাহেবই সব দেখবেন। তুই ঘরেরও হবিনে। অথচ আমায়ও মুক্তি দিবিনে। আমি কতদিন আর এ শাস্তি বইব, বল তো?’
জাহাঙ্গীর দুষ্টুমির হাসি হাসিয়া বলিল, ‘আচ্ছা মা, আমি যদি তোমার বউমা এনে দিই, তা হলে হজ করতে যেতে পারবে?’
মা যেন হাতে স্বর্গ পাইয়া বলিলেন, ‘তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক খোকা! ও অদৃষ্ট নিয়ে আমি আসিনি। বাড়িতে যদি আমার বউমা আসে, তুই ফিরে আসিস, তা হলে কাজ কী আমার মক্কার হজে! ওই হবে আমার মক্কা-কাবা সব!’
জাহাঙ্গীর হো হো করিয়া মায়ের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া বলিল, ‘বলো কী মা, তোমার বউমাই হবে সব! কাবার চেয়েও বড়ো!’ – বলিয়াই কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল, ‘থাক, আমিই বানে ভেসে এসেছিলুম!’
মা এইবার রাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, ‘চুপ কর হতভাগা ছেলে! যা নয় তাই বলা হচ্ছে!’ – বলিয়াই স্নেহ বিগলিত স্বরে বলিলেন, ‘সত্যি খোকা বল, তুই আমার ঘরে বউ এনে দিবি? আর ভূতের মতো একলা বাড়ি আগলাতে পারিনে! কেমন? তা হলে জিনিসপত্র খুলতে বলি?’ – বলিয়া হাঁক-ডাক দিতে আরম্ভ করিলেন, ‘ওরে মোতিয়া, দেওয়ানজিকে একবার খবর দে তো !’
মোতিয়া বাড়িরই পুরাতন ঝি। সে এতক্ষণ সব শুনিতেছিল আড়ালে থাকিয়া। এই খোশখবরে সে আর থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিল, ‘বেগম আম্মা, আপনি দেইহ্যা বুঝবার পারছেন না, ভাইজানের মুখ ক্যামন শুরুষকু অইয়্যা গিয়াছে! জোয়ান পোলার শাদি না দিলে সে তাই ব্যাওরা অইয়্যা যাইব না?’
জাহাঙ্গীর হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল। মা-ও হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, ‘তুই যা দেখি, আগে দেওয়ান সাহেবকে ডেকে আন, তার পর তোর ভাইজানের শাদির কথা হবে।’
জাহাঙ্গীর বলিয়া উঠিল, ‘তার আগে মা তোমার সব কথা ভালো করে শোনা দরকার!’
মোতিয়া তাহার কাজলায়িত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া জাহাঙ্গীরের দিকে তাকাইয়া চলিয়া গেল।
মাতা পুত্রের রুক্ষ চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে বলিলেন, ‘কতদিন তেল মাখিসনে খোকা, বল তো! তুই কি সন্ন্যাসী হয়ে যাবি নাকি শেষে?’
জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, ‘কিন্তু তুমি তো সন্ন্যাসী হতে দেবে না। সে যাক, তুমি যে আসল কথাটাই শুনতে চাচ্ছ না!’
মা হাসিয়া বলিলেন, ‘সে কথা না শুনেই আমি বুঝেছি। সে মেয়েটি কোথায় থাকে বল, তার পর আমার যা করবার আমি করব!’
জাহাঙ্গীর লজ্জিত হইয়া বলিল, ‘তুমি যা মনে করছ মা তা নয়। আমি তোমার কাছে কিছু লুকোব না। সব শুনে তুমি যা করতে বলবে তাই করা যাবে।’
জাহাঙ্গীর হারুণদের বাড়ি যাওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার উন্মাদিনী মাতার কীর্তি পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা বলিয়া গেল। বলিল না শুধু তাহার বিপ্লবীদলের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকার কথা।
মাতা বিস্ময়াভিভূত হইয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া কোনো কথা উচ্চারিত হইল না। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার মুখে আনন্দ ও শঙ্কার আলোছায়া খেলিয়া যাইতে লাগিল।
হঠাৎ জাহাঙ্গীর বলিয়া উঠিল, ‘কিন্তু মা তাকে কিছুতেই এ বাড়িতে আনা যেতে পারে না। তোমাকে বলতে ভুলে গেছি – সে অতিমাত্রায় অহংকারী মেয়ে। আমার মা গিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করে আনলে তবে নাকি তিনি আমাদের ঘরে শুভ পদার্পণ করলেও করতে পারেন। বিষ নেই মা, কিন্তু ফণা-আস্ফালন আছে!’
মা হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, ‘সে ঠিকই বলেছে খোকা। তা যদি সে না বলত, আমি তাকে আনবার কথা ভাবতে পারতুম না। যে সাপ ফণা ধরে – তার বিষও থাকে, সে জাতসাপ।’
জাহাঙ্গীর ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিল, ‘তুমি কি তাকে এ বাড়িতে আনবে মা?’
মা হাসিয়া বলিলেন, ‘তা আনতে হবে বইকী! খোদা নিজে হাতে যে সওগাত পাঠিয়েছেন তাকে মাথায় তুলে নিতে হবে।’
জাহাঙ্গীর ক্লান্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ‘কিন্তু মা আমি তো তাকে বিয়ে করতে পারি না। তাকে কেন, কাউকেই বিয়ে করবার অধিকার আমার নেই!’
মা চমকিয়া উঠিয়া কী ভাবিলেন। তাহার পর আদেশের স্বরে বলিলেন, ‘তোর তো বিয়ে হয়ে গেছে খোকা। তুই তাকে অস্বীকার করতে পারিস, কিন্তু সে মেয়েকে না দেখলেও তোর কাছে তার সম্বন্ধে যা শুনেছি – তাতে মনে হচ্ছে – সে তোকে অস্বীকার করতে পারবে না। তুই যদি তাকে না নিস, সে তার নিয়তিকে মেনে নিয়ে চিরকাল দুঃখ ভোগ করবে। জানি না, তার অদৃষ্টে কী আছে, কিন্তু আমার ছেলে যদি তার কাছে চির-অপরাধীই থেকে যায় আমাকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে!’
জাহাঙ্গীর শূন্যদৃষ্টিতে একবার তাহার মাতার পানে চাহিয়া অসহায়ভাবে শুইয়া পড়িল।
মা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, ‘কিন্তু তোর এত ভয় কেন খোকা? সে কি সুন্দরী নয়? না অন্য কারণে তোর মনে ধরেনি?’
জাহাঙ্গীর রুগ্ণ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, ‘না মা, তা নয়। তার মতো সুন্দরী মেয়ে খুব কমই চোখে পড়ে। তুমি তো হারুণকে দেখেছ। তার চেয়েও সে সুন্দর। আর, মনে ধরার কথাই উঠতে পারে না, কেননা সে মনই আমার নেই। আমায় বিয়ে করতে নেই – তাই বলছিলুম।’
মাতা স্থিরদৃষ্টিতে পুত্রের পানে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, ‘বিয়ে করতে নেই মানে? তুই কি ফকির-দরবেশের ব্রত নিয়েছিস?’
জাহাঙ্গীর অন্যদিকে চাহিয়া বলিল, ‘কতকটা তাই!’
মাতার দুই চোখ অশ্রুতে পুরিয়া উঠিল! তবে কি পুত্র তাহার জন্ম-কাহিনির বেদনা আজও ভুলিতে পারে নাই? আজও কি সে তার জন্মের জন্য অনুতপ্ত?
মোতিয়া আসিয়া খবর দিল, দেওয়ান সাহেব আসিয়াছেন। মাতা মোতিয়াকে বলিলেন, ‘তুই তোর ভাইজানের কাছে থাক, দেওয়ান সাহেবের সাথে আমার কথা আছে।’ বলিয়া পাশের কামরায় উঠিয়া গেলেন।
মোতিয়া জাহাঙ্গীরের পানে পৌনে দুই চোখে তাকাইয়া মুচকি হাসিয়া বলিল, ‘ভাইজান, পা টিপ্যা দিবাম নি?’
জাহাঙ্গীর কোনো উত্তর দিল না। হয়তো সে তাহার কথা শুনিতেই পায় নাই।
মোতিয়া জাহাঙ্গীরের পা কোলে তুলিয়া লইয়া টিপিতে লাগিল।
জাহাঙ্গীর আপত্তি করিল না।
তখন মনে তাহার ঝড় বহিতেছিল। তাহার মনে পড়িল, ভূণীর চিঠির কথা। পর দিন অর্থের লোভে গোরুর গাড়ির সেই গাড়োয়ান সত্যসত্যই শিউড়ি স্টেশনে পত্রের উত্তর লইয়া আসিয়াছিল।
ভূণী লিখিয়াছিল: ‘যদি মা আমাকে আপনার হাতে সঁপিয়া না দিতেন, আমি আপনার পত্রের উত্তর দেওয়া অপমানজনক মনে করিতাম! আপনি যাহাকে চিরজীবনের নির্বাসন-দণ্ড দিয়া গিয়াছেন, হঠাৎ তাহার প্রতি এই করুণার হেতু কী, জানি না। আমি আপনাকে যতটুকু বুঝিয়াছি – তাহাতে আমার ধারণা – হৃদয় ছাড়া অপনার সকল কিছুই আছে। কিন্তু সে সকল লইয়া তো – নারী আমি – আমার কোনো লাভ নাই। দুঃখের সমুদ্রে কলার ভেলায় আমরা ভাসিতেছিলাম। হঠাৎ আপনার বিপুল অর্ণবপোত আমাদের কাছে আসিল। উদ্ধার পাইবার আশা করি নাই, বরং মনে যে ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল – তাহাই ফলিয়া গেল। আপনার জাহাজের ঢেউ লাগিয়া আমাদের কলার ভেলাখানি ডুবিয়া গেল। এখন তরঙ্গের সঙ্গে যুদ্ধ করা ছাড়া অন্য পথ নাই। যতদিন শক্তি থাকিবে যুদ্ধ করিব।
আপনি কূলে উঠিয়াছেন। যাহারা তরঙ্গে ডুবিতেছে – তাহাদের লইয়া এ বিদ্রুপ কেন?
ইচ্ছা করিলেই কি আপনার কূলে উঠিতে পারি? আপনি কী ভাবিয়া আমায় ডাকিয়াছেন, জানি না।
যে অধিকার আমার মা আপনাকে দিয়াছেন – সেই অধিকারের দাবি লইয়া যেদিন শুধু আপনি নয় – আপনার অভিভাবিকা জননী আসিয়া ডাকিবেন – সেই দিন হয়তো যাইতে পারি। কিন্তু তাহার পূর্বে নয়। লোকসমাজের শ্রদ্ধা হারাইয়া আপনার কাছে গেলে – আপনিই আমায় শ্রদ্ধা করিতে পারিবেন না। অন্তরে যাহাকে স্বীকার করিয়া লইয়াছি, বাহিরের দিনের আলোকে তাহাকে স্বীকার করিবার সৌভাগ্য যদি অর্জন করি, সেদিন আপনার আদেশে আমি মৃত্যুর মুখোমুখি গিয়া দাঁড়াইতে পারিব।
আশা করি, আপনি আমায় ভুল বুঝিবেন না। এবং আর এরূপ ছেলেমানুষিও করিবেন না। আমার আত্মসম্মান আপনার আত্মসম্মানের চেয়ে কোনো অংশে হীন বা ন্যূন নহে!
বাহিরের ঐশ্বর্যের দম্ভ আমার নাই, আমরা দরিদ্র; কিন্তু অন্তরের ঐশ্বর্যের গৌরব আমার অন্তত আপনার অপেক্ষা কম নাই।
আমাদের মাঝে যে অকূল পারাবার বহিয়া চলিত – তাহাই হয়তো আমার নিয়তি।
এ কূলে আপনি আসিয়াছেন, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য বলিয়া মানিব। ও কূল হইতে আর হতছানি দিয়া ডাকিবেন না। মানুষেরই তো মন, একবার যদি ঝাঁপাইয়া পড়ি প্রলোভনের বশে এ কূল ও কূল দুই কূল হারাইব।
মা আপনার জন্য এখনও কাঁদেন। বলেন, “মিনা এসে চলে গেল! ও আর আসবে না!” যদি উপযুক্ত চিকিৎসা হইত, মা হয়তো ভালো হইলেও হইতে পারিতেন।
এইবার বাবার আর দাদার পাগল হইতে বাকি, আপনার অনুগ্রহে হয়তো তাহারও আর বিলম্ব নাই।
আপনি কি জাদু জানেন? মোমি আর মোবারক আজও আপনার ওকালতি করে! দুটো কাপড় আর দু হাঁড়ি সন্দেশের এমনই মোহ! চির-দুঃখী কিনা!
আমাকে ভুলিয়াও যে স্মরণ করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। আরও ধন্যবাদ দিব, যদি স্মরণ করিয়া ভুলিয়া যান এবং এইরূপ অসম্মানজনক পত্রাদি প্রেরণ না করেন! ইতি –
আপনার দয়া – ঋণী
তহমিনা।”
কুহেলিকা – ১৪
জাহাঙ্গীর সুখ ও দুঃখের নানা স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।
জাগিয়া দেখিল, তাহার মাতা শিয়রে বসিয়া অতন্দ্রনয়নে তাহার পানে চাহিয়া আছেন।
সে চোখ মেলিতেই মা বলিয়া উঠিলেন, ‘জেগে উঠলি খোকা? ঘুমো আরও খানিক।’
জাহাঙ্গীর উঠিয়া বসিয়া বলিল, ‘না মা, আর ঘুম হবে না।’ বলিয়াই উসখুস করিতে লাগিল।
মা হাসিয়া বলিলেন, ‘তুই কী ভাবছিস বলতো! আমি কালই হারুণের বাড়ি যাব। দেওয়ান সাহেবও যাবেন, তোকেও যেতে হবে।’
জাহাঙ্গীর কোনোরূপে শুধু বলিতে পারিল…’মা!’
মা বলিলেন, ‘হাঁ, এ তোর মায়ের আদেশ।’ বলিয়াই একটু থামিয়া বলিলেন ‘তোর পাঞ্জাবিটা ধুতে দিতে গিয়ে তার পকেটে বউমার লেখা চিঠি দেখেছি। এমন মেয়ে পেয়েও যদি তুই মাথায় তুলে না নিস, বুঝব তোর কপালে বড়ো দুঃখ আছে। তুই না নিস, আমি আমার ঘরের লক্ষ্মীকে মাথায় করে নিয়ে আসব। আমি হজ করতে যাব বলে বেরিয়েছিলুম – খোদা আমার হজের পুণ্য রাস্তাতেই দিয়েছেন। তাকে না নিতে পারলে খোদা নারাজ হবেন!’
জাহাঙ্গীর ফাঁসির আসামির মতো দয়া ভিক্ষার স্বরে বলিয়া উঠিল, ‘দোহাই মা, আমায় এত বড়ো শাস্তি দিয়ো না। এ শাস্তির অংশ তাকেও নিতে হবে তা হলে। তা ছাড়া সে যা মেয়ে – তুমি গেলেও সে আসবে না – যদি না আমি তাকে সত্যিকার বিয়ে করি।’
মা হাসিয়া বলিলেন, ‘তোর বিয়েতে এত ভয় কেন খোকা বল তো! তোকে তো কেউ ফাঁসি দিচ্ছে না!’ – বলিয়া জিভ কাটিয়া ‘ষাট ষাট বালাই’ বলিয়া পুত্রের শিরশম্বন করিয়া বলিলেন, ‘কী বদখেয়ালি কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় গো মা! – যাক, এখন যদি তুই রাজি নাই হোস – তার ব্যবস্থাও দেওয়ানজি করে রেখেছেন। হারুণকে আমার স্টেটে এখন শ-তিনেক টাকার চাকরি দিয়ে ওদের সপরিবারে কলকাতায় নিয়ে আসব। চব্বিশ পরগনায় রায়েদের একটা বড়ো জমিদারি বিক্রি হচ্ছে – সেটা কিনে নেবার ব্যবস্থা করেছি। হারুণ সেই স্টেটের ম্যানেজার হবে। তারপর যা করবার, করা যাবে।’
জাহাঙ্গীর এক মুহূর্তে সব ভুলিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, ‘সত্যি মা, তুমি হারুণকে নিয়ে আসবে? আহা, বেচারার বড়ো দুঃখ মা! এইবার বি.এ. দেবে, কিন্তু পাশ করলেও সে চাকরি পেত কোথায়? অথচ ওর চাকরি না হলে ওরা সব কটি প্রাণী উপোস করে মরবে! ওকে যদি চাকরি দিয়ে আনতে পার তা হলে আমার কৃতকার্যের অনেকটা অনুশোচনা কমে।’
মা হাসিয়া বলিলেন, ‘তোর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় বল।’– মা মনে মনে ভাবিলেন, ছেলে শুধু হারুণের চাকরির জন্যই খুশি হইয়া উঠে নাই, তাহার সাথে মেয়েটাও যে আসিবে, ইহাও তাহার খুশি হইয়া উঠার অন্যতম কারণ। তাঁহার মনের মেঘ অনেকটা কাটিয়া গেল! ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার খোকা বিবাহ ব্যাপারে অতিরিক্ত লজ্জা অনুভব করে। ওরূপ খেয়াল অনেক ছেলেরই থাকে এবং তাহা কাটিয়া যাইতেও দেরি হয় না। তাঁহার খোকাও হয়তো মনে মনে রাজি আছে, শুধু লজ্জার খাতিরে এতটা করিতেছে। তাই অত্যন্ত প্রসন্ন মনে উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, ‘বেশি রাত্রি হয়নি এখনও। এখনই আমার সব দরকারি জিনিসপত্র কিনে ফেলতে হবে, তুইও আমার সাথে চল। দেওয়ানজি গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছেন বাইরের ঘরে।’
জাহাঙ্গীর উঠিতে উঠিতে বলিল, ‘কিন্তু আমাকে আর যেতে হবে না তো সাথে?’
মা বলিলেন, ‘সে কাল সকালে বোঝা যাবে। সকালেই ট্রেন, আমি টেলিগ্রাম করে দিয়েছি হারুণের ওখানে। হারুণ শিউড়ি স্টেশনে থাকবে! তুই মুখ হাত ধুয়ে কাপড় ছেড়ে প্রস্তুত হয়ে নে, আমি আসছি!’ জাহাঙ্গীর মুখ হাত ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া চা খাইতে খাইতে নানান আকাশ-কুসুমের কল্পনা করিতে লাগিল। তাহার আর সেখানে যাওয়া উচিত কিনা। অথচ সে না গেলে যদি তাহারা আসিতে অসম্মত হয়। সত্যই তাহার পাপের যদি কিছু মাত্রও প্রায়শ্চিত্ত হয় হারুণকে দারিদ্রের কবল হইতে রক্ষা করিয়া, তাহা হইলেও তাহার যাওয়াই উচিত। কিন্তু তাহাকে দেখিয়া যদি আবার ভূণীর অভিমান উথলিয়া উঠে! হারুণই যদি এই অনুগ্রহ লইতে অসম্মত হয়! তাহার পিতা যদি পৈতৃক ভিটা ছাড়িয়া আসিতে না চান। কিন্তু এ সকলের ঊর্ধ্বে সে তাহার বুদ্ধিমতী মাতার স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের ও দেওয়ান সাহেবের বৈষয়িক বুদ্ধির উপর বেশি ভরসা রাখে। তাঁহারা ইহার একটা কিনারা করিয়া উঠিতে পারিবেন নিশ্চয়। কিন্তু তবু ওই দলিতা নাগিনির মতো তহমিনা? সে যদি ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়! হঠাৎ জাহাঙ্গীরের চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। না, তাহার কিছুতেই যাওয়া হইতে পারে না। মাতা যাইতেছেন, যান, সে অপমানিত হইতে কিছুতেই সেখানে যাইবে না!
মাতা আসিয়া বলিলেন, ‘খোকা ওঠ, রাত্রি সাড়ে আটটা বেজে গেল। দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাবে আবার।’
জাহাঙ্গীর সুবোধ বালকের মতো মাতার সহিত গিয়া গাড়িতে বসিল। দেওয়ানজি অন্য গাড়িতে উঠিলেন।
মাতার বাজার করিবার ঘটা দেখিয়া জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, ‘মা, তুমি যে জুয়েলারির আর কাপড়ের দোকান উজাড় করে নিয়ে যাবে দেখছি!’
মা হেসে বলিলেন, ‘এতদিন পরে মেয়ে পেলুম, তাকে দেবার মতন গয়না-কাপড় কি তবু পাওয়া গেল! তুই ওকে যা দুঃখ দিয়েছিস, এত গয়না-কাপড় দিয়েও তো তা ঢাকতে পারব না খোকা!’
জাহাঙ্গীর আর কোনো কথা বলিতে সাহস করিল না।
দেওয়ান সাহেবের ভ্রুকুটি মুখেও খুশি যেন আর ধরে না। ফররোখ সাহেব শুধু তাঁহার প্রভু ছিলেন না, তাঁহার প্রিয়তম বন্ধুও ছিলেন। তিনি বাঁচিয়া থাকিতে এবং আজও দেওয়ান সাহেব কোনোদিন ভাবিবার অবকাশ পান নাই যে, তিনি বেতনভোগী ভৃত্য। পরম বিশ্বাসে তাঁহার হাতে জমিদারির সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করিয়া ফররোখ সাহেব আনন্দ করিয়া কাটাইয়াছেন। জাহাঙ্গীরের মাতাও তেমনি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা সহকারে দেওয়ান সাহেবকে সম্মান করিয়া আসিতেছেন। দেওয়ান সাহেবের দুইটি পুত্র। দুইটি পুত্রই বিলাতে গিয়াছে। বন্ধুজ ও প্রভুপুত্র জাহাঙ্গীরকে পুত্রাধিক স্নেহের চক্ষে দেখিতেন বলিয়াই তাহার ভাবী সুখের সম্ভাবনায় এতটা উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছেন।
এত বড়ো বিষয়ী ও মিতব্যয়ী দেওয়ান সাহেবও সেদিন যেন অতি বড়ো অমিতব্যয়ী হইয়া উঠিলেন। জাহাঙ্গীর ইহা লইয়া একবার বলিয়া ফেলিল, ‘আজ দেওয়ান সাহেবের আঙুলগুলো অতিরিক্ত ফাঁক হয়ে গেছে! যে আঙুল দিয়ে কখনও জল গলেনি, সেই আঙুলের ফাঁক দিয়ে হাজার হাজার টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে!’
দেওয়ানজি শুনিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, ‘কিন্তু এ টাকা তো জলে পড়ছে না বাবাজি! যার টাকা তাকেই দিচ্ছি। এই জমিদারিই দু-দিন পরে যার কাছে বিকিয়ে দিতে যাচ্ছি, এই দু-দশ হাজার টাকা নজরানাও তার কাছে কিছুই নয়। তুমি তো জমিদারি দেখলে না বাবা, এইবার যে দেখবে – তাকে এ কয়-টাকার জিনিস আর দিলুম?’
জাহাঙ্গীরের মাতা অশ্রুভারাক্রান্ত কণ্ঠে বলিলেন, ‘তুই কী বলছিস খোকা, তোর বাবা মরবার সময় যে ওই দেওয়ানজির হাতেই তোকে দিয়ে গেছিলেন । আজ তোর আনন্দের দিনে উনি কি হিসেব করে আনন্দ করবেন?’
পরদিন সকালে হাওড়া প্ল্যাটফর্মে স্তূপীকৃত হইয়া উঠিল রাশি রাশি জিনিসপত্র একটা স্যালুনের সামনে! দেওয়ানজি প্ল্যাটফর্মে ছুটাছুটি করিয়া চেঁচাইয়া হইচই বাধাইয়া তুলিলেন।
জাহাঙ্গীর কলের পুতুলের মতো দেওয়ান সাহেব ও তাহার মাতার আদেশ পালন করিয়া যাইতে লাগিল। স্টেশনে হঠাৎ এক জন মউলবি সাহেব চলিয়া যাইতে যাইতে যেন জাহাঙ্গীরকে ছড়ির মৃদু আঘাত করিয়া গেল। জাহাঙ্গীর ফিরিয়া দেখিবামাত্র মউলবি সাহিব ইঙ্গিতে তাহাকে ডাকিলেন। কাছে যাইতেই মউলবি সাহেব বলিলেন ‘আমি সব জানি। শিউড়িতে নেমে আমার সাথে দেখা করিস। আমিও সেখানেই নামব।’
জাহাঙ্গীর হাসিয়া নমস্কার করিতে গিয়া সামলাইয়া লইয়া আদাব করিয়া চলিয়া আসিল।
মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘উনি কে খোকা?’
জাহাঙ্গীর বলিল, ‘উনি আমাদের কলেজের আরবির প্রফেসর। উনিও শিউড়ি যাচ্ছেন, তাই আমায় শিউড়িতে নেমে দেখা করতে বললেন।’
মাতা আর প্রশ্ন করিলেন না। জাহাঙ্গীর তাহার প্রমতদার এই হঠাৎ আবির্ভাবে একটু চিন্তান্বিত হইয়া পড়িল। সে হঠাৎ এই ভাবিয়া খুশি হইয়া উঠিল, যে সুখের স্বর্গ সে রচনা করিতে চলিয়াছে – এইবার তাহা হয়তো তাহার অদৃশ্য ভাগ্যদেবতার রুদ্র আশীর্বাদে আগুনে পুড়িয়া যাইবে।
মাতা হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, ‘খোকা, তোর মউলবি সাহেবকে আমাদের স্যালুনেই ডেকে নে না। দেওয়ান সাহেবের কামরায় তিনি থাকবেন। যা, ডেকে এনে খেতেটেতে দে।’
জাহাঙ্গীর প্রমাদ গণিল! তাহার মনে হইল মাতা বোধ হয় সন্দেহ করিয়াছেন।
সে বলিল, ‘আর তো ট্রেন ছাড়বার সময় নেই মা। ওঁকে বরং বর্ধমান স্টেশনে ডেকে নেব আমাদের গাড়িতে।’
মাতা বলিলেন, ‘না, না, যথেষ্ট সময় আছে! এখনও আধ ঘণ্টা দেরি। ভদ্রলোকের হয়তো কত কষ্ট হবে। তিনি তোর মাস্টার, কী মনে করবেন বল তো! তা ছাড়া ওঁকে দিয়ে আমার কাজ আছে।’
জাহাঙ্গীর একেবারে ভয় খাইয়া গেল। পাছে মাতার সন্দেহ আরও বাড়ে, তাই সে দ্বিরুক্তি না করিয়া মউলবি সাহেবকে খুঁজিতে নামিয়া গেল।
জাহাঙ্গীর অহেতুক ভয়চিত্ত। তাহার তথাকথিত মউলবি সাহেবকে বলিতেই তিনি সানন্দে দেওয়ান সাহেবের গাড়িতে আসিয়া বসিলেন এবং বিনা ওজরে খাদ্যাদির সৎকার করিলেন।
জাহাঙ্গীর অহেতুক ভয়চিত্ত। তাহার তথাকথিত মউলবি সাহেবকে বলিতেই তিনি সানন্দে দেওয়ান সাহেবের গাড়িতে আসিয়া বসিলেন এবং বিনা ওজরে খাদ্যাদির সৎকার করিলেন।
দেওয়ান সাহেব মউলবি সাহেবের সাথে জাহাঙ্গীরের কথা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন। জাহাঙ্গীর দেখিল, তাহার প্রমতদা নকল মউলবি হইলেও আসল মউলবির চেয়েও দুরস্ত-জবান। চমৎকার উর্দু-ফারসির আমেজ দিয়া তিনি কথা বলিতেছেন।
পাশের কামরা হইতে জাহাঙ্গীরের মাতা বাঁদি দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, মউলবি সাহেবকেও তাহাদের এই খুশিতে শরিক হইতে হইবে। অর্থাৎ তাহাদের সাথে তাঁহাকেও যাইতে হইবে।
মউলবি সাহেব বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি অবশ্যই হুজুর আম্মার এ হুকুম পালন করিতেন যদি না শিউড়িতে তাঁহার রোগ-শায়িতা বহিনকে দেখিতে না যাইতেন!
মউলবি সাহেব জাহাঙ্গীরকে এক সময় একলা পাইয়া চুপি চুপি বলিলেন, ‘তোদের স্যালুনে জায়গা গেয়ে আমার ভালোই হল, শালার টিকটিকি আর পিছু নিতে পারবে না!’
জাহাঙ্গীর প্রশ্ন করিল, ‘কিন্তু প্রমতদা, আমার কী হবে? আমাকে যে যূপকাষ্ঠে নিয়ে যাচ্ছে!’
মউলবি সাহেব হাসিয়া বলিলেন, ‘খোদার মর্জি বাচ্চা! সব মেঘ কেটে যাবে! মাকে অসন্তুষ্ট কোরো না, খোদার রহম আপনি তোমার ওপর নাজেল হবে!’
জাহাঙ্গীর হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, ‘সোবহান আল্লাহ্ মউলবি সাহেব! ক্যা তরিকা বাতায়া আপনে!’
মউলবি সাহেব এধার ওধার দেখিয়া লইয়া বলিলেন, ‘তোকে পিনাকীর মাসিমা ডেকেছেন, তা ছাড়া আমারও কাজ আছে। তুই হারুণের বাড়ির ফেরতা ওখান হয়ে যাবি।’
জাহাঙ্গীর বলিল, ‘কিন্তু মা যে সাথে আছেন!’
মউলবি সাহেব বলিলেন, ‘তার ব্যবস্থা করা যাবে খন।’
গাড়ি ছাড়িয়া দিল। জাহাঙ্গীরের বুক অজানা অশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল।
কুহেলিকা – ১৫
বর্ধমান স্টেশনে নামিয়া জাহাঙ্গীর মউলবি সাহেবকে লইয়া ‘রিফ্রেশমেন্ট রুমে’ ঢুকিয়া পড়িল।
সৌভাগ্যবশত তাহারা দুই জন ছাড়া আর কেহ সেখানে ছিল না।
মউলবি সাহেব বলিলেন, ‘মামারা এখনও মুসলমানকে সন্দেহের চক্ষে দেখে না, তাই আজও দিনের আলোকে কোনোরকমে মউলবি সাহেব সেজে বেড়াচ্ছি। কিন্তু সে কথা যাক, তোর ওপর আবার ভীষণ কাজের ভার পড়বে, পারবি?’
জাহাঙ্গীর বলিল, ‘এর মধ্যে তো পারা-না-পারার কথা নেই। যা আদেশ করবেন, তা আমায় পালন করতেই হবে।’
মউলবি সাহেব খুশি হইয়া বলিয়া উঠিলেন, ‘জিতা রহো লেড়কা! তোকে আবার মালপত্র সরিয়ে নিয়ে আসতে হবে। তুই ছাড়া এ-কাজ আর কারুর দ্বারাই হবার নয়।’
জাহাঙ্গীর বলিল, ‘সেবার কিন্তু মরতে মরতে বেঁচে গেছি দাদা! আবগারি সাব-ইন্স্পেকটার যখন গাড়িতে উঠে বাক্স-প্যাঁটরা খুলতে আরম্ভ করলে, তখন আমার আত্মারাম তো খাঁচা-ছাড়া হবার যো হয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে এক জনের প্যাঁটরা থেকে সের কতক আফিম বেরোতেই সে তাকে পাকড়াও করে নেমে গেল। একে একে সব বাক্স যদি খুঁজত, কী হত তাহলে ভাবতেও গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠে!’ বলিয়াই সামলাইয়া লইল, ‘ভাবনা আমার নিজের জন্য ছিল না – ভাবনা ছিল জিনিসপত্রগুলো নিয়ে। সে ব্যাটাও মরত – হয়তো বা আমিও মরতুম – মাঝে অত দামি জিনিসগুলো বেহাত হয়ে যেত!’
মউলবি সাহেব বলিলেন, যাক এবার তোদের স্যালুনেই ওগুলো নিয়ে যেতে পারবি ফিরে যাবার সময়। কারুর কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকবে না।
জাহাঙ্গীর হঠাৎ অপ্রসন্ন হইয়া বলিয়া উঠিল, ‘কিন্তু এবার যে আমার বোধ হয় জোড়ে ফিরতে হবে দাদা!’
মউলবি সাহেব বলিলেন, ‘দেখ – নিয়তিকে এড়াতে পারবিনে। আমাদের বজ্রপাণিও তো বিবাহিত। শুধু বিবাহিতই নন, ছেলে-পিলে ঘর-সংসার আছে। আসল কথা, তোর যদি সত্যকার দেশপ্রেম থাকে – কোনো ব্যাটাই তোর সামনে দাঁড়াতে পারবে না।’
গাড়ি ছাড়িবার ঘণ্টা পড়িতেই, তাহারা তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। উঠিতে দরজার সামনে এক চিরপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিয়া জাহাঙ্গীর থতমত খাইয়া গেল। এ যে সেই ধাড়ি টিকটিকি অক্ষয়বাবু! জাহাঙ্গীরের অবস্থা বুঝিয়াই যেন মউলবি সাহেব কাংস্য কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, ‘আরে বেহোঁশ! আভি টারিন ছোড় দেগা! দৌড়কে চল!’
অক্ষয়বাবু বাজপাখির মতো চোখে তাহাদের দিকে তাকাইয়া থাকিলেন।
জাহাঙ্গীরকে দেখিয়া অক্ষয়বাবুও পাশের গাড়িতে উঠিয়া পড়িল।
জাহাঙ্গীর ইঙ্গিত করিতেই মউলবি সাহেব বলিয়া উঠিলেন, ‘কুছ ফিকির নেই বাচ্চা, উয়ো হজম হো যায়েগা।’
দেওয়ান সাহেব হাসিয়া বলিলেন, ‘আর একটু দেরি হলেই স্টেশনে বসে বসে হজম করতে হত মউলবি সাহেব। আর আপনারা নামবেন না কোথাও! গাড়িতেই খাবার আনিয়ে নেবেন!’
অণ্ডাল স্টেশনে গাড়ি বদল করিবার সময় জাহাঙ্গীর দেখিল, অক্ষয়বাবু তাহাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেছেন। সেদিকে আর বেশি দৃষ্টিপাত না করিয়া একটা বই লইয়া পড়িতে লাগিল। তাহাদের গাড়ি হইতে নামিবার ঝঞ্ঝাট পোহাইতে হইল না। তাহাদের স্যালুন ইঞ্জিন আসিয়া টানিয়া শিউড়ির গাড়ির ন্যাজে জুড়িয়া দিল।
মউলবি সাহেব হাসিয়া বলিলেন, ‘অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না, গানটা জান?’
জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, ‘গানটা জানি, কিন্তু গাইতে জানি না। আর জানলেও গাইতাম না।’
পাশের কামরা হইতে মা বলিয়া উঠিলেন, ‘খোকা বুঝি গান-টান একেবারে ভুলে গেছিস?’
জাহাঙ্গীর বলিল, ‘হাঁ, মা, ওসব ভুলে যাওয়াই ভালো। অনর্থক কতকগুলো লোকের শান্তিভঙ্গ করে লাভ কী?’
মা হাসিয়া বলিলেন, ‘গানে বুঝি শান্তিভঙ্গ হয়? তুই একেবারে ভূত হয়ে গেছিস খোকা! দুনিয়ায় কি তোর সব আশা-আকাঙ্ক্ষা মিটে গেছে এরই মধ্যে?’
জাহাঙ্গীর হাসিয়া আস্তে আস্তে বলিল, ‘বেটি ভয়ানক চালাক! পাশের জানলায় বসে শুনছেন আমরা কী কথা বলা-কওয়া করি!’
সন্ধ্যায় ট্রেন শিউড়ি আসিয়া পঁহুছিল।
হারুণ ছুটিয়া আসিয়া জাহাঙ্গীরের মাতার ও দেওয়ান সাহেবের পায়ের ধুলা লইল। মাতা তাহাকে জাহাঙ্গীরের মতোই বুকে ধরিয়া শিরশ্চুম্বন করিলেন।
দেওয়ান সাহেব এক ডজন কুলি লইয়া জিনিসপত্র নামাইতে লাগিলেন।
হঠাৎ মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘খোকা, তোর মউলবি সাহেব কোথায় গেলেন?’
জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, ‘উনি এতক্ষণ বোধ হয় তাঁর বোনের বাড়িতে গিয়ে উঠেছেন মা!’
মাতা বলিলেন, ‘সে কী! তুই ওঁর বোনের বাসা চিনিস? সেখান থেকে তাঁকে যে আনতেই হবে!’
জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, ‘সে তো আমি চিনি না মা। তা ছাড়া ওঁর বোনের অসুখ, এখন তো যেতেও পারতেন না।‘
হারুণ জিজ্ঞাসা করিল, ‘কোন মউলবি সাহেব?’
জাহাঙ্গীর বলিল, ‘প্রফেসার আজেহার সাহেব।’
হারুণ বলিল, ‘কই তাঁকে তো দেখলুম না।’
জাহাঙ্গীর বলিল, ‘তোমরা যতক্ষণ বোঁচকা-পুটুলি সামলাচ্ছিলে, ততক্ষণ উনি পগার পার হয়ে গেছেন।’
জাহাঙ্গীর দেখিল, অক্ষয়বাবু সারা প্ল্যাটফর্ম মন্থন করিয়া ফিরিতেছেন! সে অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিয়া মনে মনে বলিল, ‘ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি।’
তবু তাহার মনে কেমন একটা অজানা ভয় উঁকি দিয়া ফিরিতে লাগিল।
গোটা চার পালকি ও দুইখানা গোরুর গাড়ি বোঝাই হইয়া জিনিসপত্র সমেত সদলবলে জাহাঙ্গীর হারুণের গ্রামে যাত্রা করিল।
টর্চলাইট ও বন্দুক সাথে ছিল। তাহা ছাড়াও চারি বেহারার পালকি, গাড়োয়ান, ভোজপুরি বরকন্দাজ প্রভৃতির জন্য কেহ আর রাত্রে যাইতে আপত্তি করিল না। আকাশও বেশ পরিষ্কার ছিল, ঝড়-বৃষ্টির কোনো সম্ভাবনা ছিল না। নিদাঘের সুনির্মল আকাশে শুক্লা নবমীর চাঁদ শুক্লা নবমীর চাঁদ ঝলমল করিতেছিল।
পালকিতে উঠিয়া জাহাঙ্গীরের মাতা বলিলেন, ‘বাবা! এ রকম বাক্সবন্দি হয়ে যাওয়ার তো অভ্যাস নেই। একে এই গরম, তার ওপর এইরকম ঘাড়মুড় ভেঙে বসে থাকা। আমি তাই বলছিলাম মোটরটা সাথে আনতে।’
হারুণ হাসিয়া বলিল, ‘মোটর না এনে ভালোই করেছেন মা। এ দেশে মোটর যাবার রাস্তা নেই। তার ওপর মাঝে নদী।’
বিচিত্র শব্দ করিতে করিতে পালকি-বাহকগণ অগ্রে অগ্রে চলিল। পশ্চাতে গোরুর গাড়ি, সকলের শেষে বন্দুক স্কন্ধে বরকন্দাজ।
রাত্রি প্রায় এগারোটার সময় সকলে হারুণদের গ্রামে গিয়া পঁহুছিলেন। পল্লিগ্রামে রাত্রি এগারোটার সময় কেহ সজাগ ছিল না। বেগম দেখিতে হয়তো গ্রামের লোক ভাঙিয়া পড়িত। হারুণ তাহার পিতা ও বোনদের ছাড়া কাহাকেও এ খবর বলে নাই, কাজেই গ্রামেও এ সংবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়িতে পারে নাই। মোবারক তাহার এক বন্ধুকে এই খবর বলায় সে বিদ্রুপ করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল, উপরন্তু তাহার মাথায় জোর চাঁটি মারিয়া বলিয়াছিল যে, তাহারও পাগল হইবার আর দেরি নাই। ইহার পর সে আর কাহাকেও এ খোশখবর দিতে সাহস করে নাই।
এত পালকি এত লোকজন দেখিয়া মোবারক ভ্যাবাচাকা খাইয়া প্রস্তরবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। মনে হইল, তাহার আক্কেল গুড়ুম হইয়া গিয়াছে। তাহার অন্ধ পিতা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ছুটাছুটি করিতে গিয়া দুইবার আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেলেন। হারুণ তাহার পিতাকে স্থির হইতে বলিয়া জাহাঙ্গীরের মাতাকে সসম্মানে বাড়ির ভিতর লইয়া গেল। দেওয়ান সাহেব বাহির বাড়িতে গিয়া বসিলেন।
জাহাঙ্গীর সামনের খোলা মাঠে বসিয়া হাওয়া খাইয়া বাঁচিল।
তহমিনা ও মোমি আসিয়া জাহাঙ্গীরের মাতার কদমবুসি করিল। মাতা দুই বোনকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ললাট-চুম্বন করিলেন।
বাঁদিদের হাতে টর্চ-লাইট ছিল, তাহারই আলোকে মাতা অনিমেষ নেত্রে তাঁহার ভাবী বধূর মুখ দেখিতে লাগিলেন। হ্যাঁ, তাঁহার পুত্রবধূ হবার মতো রূপসি বটে!
মাতা বারেবারে তহমিনার ললাট, চিবুক ও শিরশ্চুম্বন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অত্যধিক আদরে, কিংবা কেন জানি না, তহমিনা তাঁহার বুকে মুখ রাখিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল।
মা আঙিনাতেই দাঁড়াইয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন, ‘কেঁদো না মা আমার, সোনা আমার! আর ভয় কী! ও পাগল তোমার অসম্মান করেছে – আমি তোমাকে বুকে তুলে নিতে এসেছি।’
অনেকক্ষণ কাঁদিয়া তহমিনা শান্ত হইল। ভাগ্যক্রমে তাহার উন্মাদিনী মাতা তখন অঘোরে ঘুমাইতেছিলেন, নইলে তিনি হয়তো তাঁহার মিনার জন্য কাঁদিয়া কাটিয়া একাকার করিতেন।
বাড়ির অবস্থা দেখিয়া জাহাঙ্গীরের মাতার বুঝিতে বাকি রহিল না-দুরবস্থার শেষতম স্তরে ইহারা আসিয়া পড়িয়াছে। তাঁহার চক্ষে জল ভরিয়া আসিল। এমন সোনার চাঁদ মেয়েও এমন ঘরে থাকে!
তহমিনা সকলের জন্য রাঁধিয়া রাখিয়াছিল, সকলে তাহা খাইয়া তাহার রান্নার অশেষ তারিফ করিতে লাগিলেন।
হারুণের পিতা কেবলই বলিতে লাগিলেন, এ গরিবের বাড়ি হাতির পা পড়িবে – ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তাহাদিগকে বসিতে দিবার মতো তাঁহার স্থান তো নাই। তাঁহার বিনয় ও অসোয়াস্তি দেখিয়া দেওয়ান সাহেব এবং বেগম সাহেবা ঘনিষ্ঠ আলাপ আপ্যায়নে তাঁহাকে আপন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। হারুণের পিতা আনন্দে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন।
জাহাঙ্গীরের মাতা নিজে তহমিনা, মোমি ও মোবারককে খাওয়াইলেন। অত্যাধিক গরম পড়ায় তাঁহার সাথে দুইখানা ক্যাম্পখাট খুলিয়া উঠানেই শুইয়া পড়িলেন। তহমিনাকে পাশের খাটে শোয়াইয়া আদর করিতে করিতে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া তাহার মনের কথা বাহির করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।
তহমিনা জীবনে এত স্নেহ পায় নাই। সে এই আদরে গলিয়া গিয়া ছোটো খুকিটির মতো তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া শুইয়া দুই একটি কথায় তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিল।
দেওয়ান সাহেব হারুণের পিতার মনোভাব বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সে রাত্রে আর বেশি কথা হল না। পথশ্রান্তিতে সকলেই শীঘ্র ঘুমাইয়া পড়িল।
তহমিনার চক্ষে ঘুম ছিল না। সে যখন দেখিল, সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, অথচ তাহার ঘুম আসিতেছে না, তখন সে উঠিয়া উন্মাদিনী মাতার খোঁজ লইতে গেল। উঠান হইতে অন্দরে যাইবার পথেই সদর দরজা। সে দেখিল, সদর দরজা খোলা রহিয়াছে। দরজা বন্ধ করিতে গিয়া হঠাৎ তাহার সামনে মাঠের উপর দৃষ্টি পড়িল। দেখিল, অস্তমান চন্দ্রের ম্লান চন্দ্রালোকে বসিয়া জাহাঙ্গীর আকাশের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া আছে। সে আর চোখ ফিরাইতে পারিল না, নির্নিমেষ নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া রহিল।
কেন সে অতন্দ্রনয়নে একা জাগিয়া শূন্য আকাশে চাহিয়া আছে? এই সুন্দর পৃথিবীতে কী তাহার চাহিবার কিছুই নাই। এত ঐশ্বর্য, এমন মা যাহার তাহার কেন এই দুঃখ-বিলাস?
তহমিনা বুঝিতে পারিয়াছিল, কেন হঠাৎ জাহাঙ্গীরের মাতা সদলবলে আসিয়া হাজির হইয়াছেন। তাহার আরও মনে হইতে লাগিল, হয়তো জাহাঙ্গীরই তাহার মাতাকে লইয়া আসিয়াছে। ভাবিতেই তাহার মন অভূতপূর্ব আনন্দে কানায় কানায় পুরিয়া উঠিল। তাহা হইলে, যতটা হৃদয়হীন সে জাহাঙ্গীরকে মনে করিয়াছিল, ততটা হৃদয়হীন সে নয়!
কিন্তু কী রকম বদরসিক লোকটা? একবারও কি ভুলিয়া খোলা দরজার দিকে তাকাইতে নাই?
সে যেন দরজা বন্ধ করিবার জন্যই দুই কবাটে আঘাত করিল এবং যুগল কবাটের স্বল্প অবকাশ দিয়া দেখিতে লাগিল, জাহাঙ্গীরের ধ্যান ভঙ্গ হইয়াছে কিনা।
জাহাঙ্গীর দরজার দিকে তাকাইল এবং একজন দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে ইহাও বুঝিতে পারিল। সে মনে করিল, কোনো প্রয়োজনে হয়তো তাহার মাতা তাহাকে ডাকিতেছেন। সে দরজা ঠেলিতেই তহমিনাকে দেখিয়া চমকাইয়া প্রশ্ন করিল, ‘কে? ভূণী? আমায় ডাকছিলে?’
ভূণী ওরফে তহমিনা লজ্জায় মরিয়া গিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দাঁড়াইয়া রহিল, ছি ছি, একী বেহায়াপনা সে করিল!
জাহাঙ্গীর আবার প্রশ্ন করিল, ‘আমাকে কি কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবে?’
ভূণী হঠাৎ যেন কূল পাইল। সে অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জোরে সহজ হইবার চেষ্টা করিয়া প্রশ্ন করিল, ‘আবার এলেন কেন জিজ্ঞাসা করতে পারি?’
জাহাঙ্গীর আহত হইয়া তাহার চোখে চোখ রাখিয়া বলিল, ‘আমি তো আসিনি, মা এসেছেন তোমায় নিয়ে যেতে!’
তহমিনা জিজ্ঞাসা করিল, ‘মা তা হলে সব শুনেছেন?’
জাহাঙ্গীর ম্লান হাসিয়া বলিল, ‘শুনেছেন নয় – জেনেছেন তোমার চিঠি পড়ে!’
তহমিনা লজ্জায় মরিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, ‘মা গো কী হবে! ছি ছি! তুমি চিঠি দেখালে কেন?’
জাহাঙ্গীর এইবার একটু জোরেই হাসিয়া ফেলিল।
তহমিনা উত্তেজনায় জাহাঙ্গীরের মুখের কাছে হাত আনিয়া সহসা থামিয়া গিয়া বলিয়া উঠিল, ‘দোহাই! অত জোরে হেসো না, কেউ জেগে উঠবে।’
জাহাঙ্গীরের মনে নেশা ধরিয়াছিল। সে আয়তচক্ষু মেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ‘তুমি যাবে তো?’
তহমিনা লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলিল, ‘সে তো আপনিই জানেন!’
জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, ‘বাঃ রে! বেশ তো! একবার “আপনি!” একবার “তুমি” একবার “হিঁয়া আও” –একবার “ভাগো”!’
জাহাঙ্গীরের মাতা পাশ ফিরিয়া শুইতেই তহমিনা তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেই অসাবধানে তাহার হাতের একটা আঙুল দুই দরজার মাঝখানে পড়িয়া পিষ্ট হইয়া গেল। সে ক্ষীণ আর্তনাদ করিয়া বসিয়া পড়িল।
জাহাঙ্গীর তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া প্রশ্ন করিল, ‘কী হল ভূণী? কিছুতে কামড়েছে?’
ভূণী সে স্পর্শে কন্টকিত হইয়া মনে মনে বলিল, ‘কামড়েছে বিষধর সাপে!’ বাহিরে বলিল, ‘আঙুলটা দরজায় বড্ড চিপে গেছে!
জাহাঙ্গীর ক্ষীণ চন্দ্রালোকেও দেখিতে পাইল সত্যসত্যই আঙুলটা নীল হইয়া উঠিয়াছে। সে ভূণীর হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইল।
সে তাড়াতাড়ি আঙুলটা লইয়া চুষিতে চুষিতে বলিল, ইস! রক্ত জমে নীল হয়ে গেছে! একটু ভিজে ন্যাকড়া আনতে পার?’
তহমিনা তাহার অঙ্গুলিতে জাহাঙ্গীরের উত্তপ্ত মুখের শোষণ যতই অনুভব করিতেছিল, ততই পুলকে তাহার অঙ্গ শিথিল হইয়া আসিতেছিল। সে আর থাকিতে পারিল না – মূর্চ্ছিতার মতো জাহাঙ্গীরের অঙ্গে হেলিয়া পড়িল। জাহাঙ্গীর দিশা হারাইল। বক্ষে তহমিনার তপ্ত কোমল বক্ষের স্পর্শ পাইতেই তাহার রক্তে যেন তাহার পিতার লালসা বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল।
সে জীবনে সংযম হারায়নি, আজ সে সংযম হারাইল। তহমিনাকে বিপুল আবেগে বক্ষে অজস্র পিষিতে পিষিতে জাহাঙ্গীর তাহার নিষ্কলঙ্ক গণ্ড অজস্র চুম্বন-কলঙ্কে ভরিয়া দিল।
তহমিনা সুখে, লজ্জায়, উত্তেজনায় শিথিল-তনু শিথিল-বসন হইয়া পড়িল। সে কিছুতেই যেন নিজেকে সংবরণ করিতে পারিতেছিল না। মনে হইল তাহার নড়িবার শক্তিটুকু পর্যন্ত কে হরণ করিয়া লইয়াছে! শুধু তাহার দুই বাহু দিয়া প্রাণপণ শক্তিতে জাহাঙ্গীরের কণ্ঠ জড়াইয়া একবার অস্ফুট মিনতি করিল।
দেবকুমার এক মুহূর্তে রক্ত-লোলুপ পশু হইয়া উঠিল!
তহমিনা এইবার যেন কতকটা তাহার অবস্থা বুঝিতে পারিল। সে তাহার শিথিল বাহু দিয়া এক একবার বিবসন-অঙ্গ আবৃত করিতে ও এক একবার জাহাঙ্গীরকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু সেও আর পারিল না। অনাস্বাদিতপূর্ব উন্মাদনায় তাহারও দেহ যেন টনটন করিয়া উঠিল। সে আর বাধা দিতে পারিল না। জাহাঙ্গীরের বক্ষতলে বহুক্ষণ অজ্ঞানবৎ পড়িয়া থাকিয়া তহমিনা উঠিয়া দাঁড়াইল। বস্ত্র সংবরণ করিতে করিতে সে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, এ কী সর্বনাশ করলে তুমি আমার? আমি কী করে মুখ দেখাব কাল?
জাহাঙ্গীর কোনো উত্তর না দিয়া মাতালের মতো টলিতে টলিতে চলিয়া গেল।
এ কী করিল সে? পঙ্কজ হইলেও নিজেকে পঙ্কের ঊর্ধ্বে শতদলের মতো তুলিয়া ধরিবার তপস্যা সে করিতেছিল। তাহার যে স্বদেশ-মন্ত্রের পবিত্র অগ্নিতে অগ্নিশুদ্ধি হইয়া গিয়াছে! স্বর্গে আরোহণ করিতে করিতে এ কোন রসাতলে সে পতিত হইল! অনুতাপে অনুশোচনায় তাহার আত্মহত্যা করিবার এচ্ছা করিতে লাগিল! কিন্তু এ কী! এক মুহূর্তে সে যেন অতি বড়ো কাপুরুষ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার এখন মৃত্যুকে ভয় হইতেছে! আর সে অসংকোচে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইতে পারে না! সে তো তহমিনার সর্বনাশ করে নাই, সর্বনাশ করিয়াছে সে নিজের।
জাহাঙ্গীর মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া অসহায় শিশুর মতো রোদন করিতে লাগিল।
হঠাৎ কাহার শীতল স্পর্শে সে চমকিয়া চাহিয়া দেখিল – একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপ তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে। সে শুনিয়াছিল, এ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে সাপের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব।
সে মনে করিল, স্বয়ং বিধাতা বুঝি তাঁহার দণ্ড প্রেরণ করিয়াছেন। সে নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িয়া রহিল। তাহার অঙ্গ বহিয়া সাপ চলিয়া গেল।
তবে কি মৃত্যুও তাহাকে ঘৃণা করে? ক্লান্ত হইয়া সে সেইখানেই ঘুমাইয়া পড়িল।
কুহেলিকা – ১৬
সকালে উঠিয়া ভূণীর মনে হইল, তাহার সকল দর্পের অবসান হইয়াছে। আজ সে পথের ভিখারিনি। দুই হাত পাতিয়া এখন তাহাকে ভিক্ষার তণ্ডুলকণা গ্রহণ করিতে হইবে। কালও সে মনে করিয়াছিল, যত বড়ো দরিদ্র হোক তাহারা, তবু সে দেখাইয়া দিবে – আত্মসম্মান শুধু ধনীরই একচেটিয়া নয়। দারিদ্রের কঠিন দর্প দিয়াই সে ধনীর ঐশ্বর্যকে অতি বড়ো আঘাত করিবে।
আজ কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল, আঘাত তো সে আর করিতেই পারিবে না, উলটো যত আঘাতই আসুক, – তাহাকে পড়িয়া পড়িয়া তাহা সহিয়া যাইতে হইবে।
হারুণ ফিরদৌস বেগম সাহেবার তার পাইয়া তাহার বাবাকে জানাইবামাত্র – তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া বলিয়াছিলেন, ‘বাবা, এতদিনে খোদা মুখ তুলে চেয়েছেন!’ ভূণীর মাথায় হাত রাখিয়া অশ্রুসিক্ত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন, ‘রাজরানি হয়ে আমাদের ভুলে যাসনে মা!’
ভূণী কিন্তু কঠোর কণ্ঠে বলিয়াছিল, ‘তাঁরা নিতে এলেও আমি তোমায় ছেড়ে যাব না তো বাবা!’
পিতা বুঝিতে না পারিয়া বলিয়াছিলেন, ‘সে কী মা! হাতের লক্ষ্মীকে কি পায়ে ঠেলতে হয়? অতবড়ো জমিদারি, বেগম নিজে আমার বাড়ি আসছেন – এ কী আমার কম সৌভাগ্য?’
ভূণী রাগ করিয়া বলিয়াছিল, ‘তুমি ভুলে যাচ্ছ বাবা, আমার বাপ দাদার আজ অর্থ না থাকলেও বংশ-গৌরবে তাঁরা তাঁদের চেয়ে অনেক বড়ো। বাড়ি বয়ে তাঁরা তাঁদের ঐশ্বর্যের দর্প দেখাতে আসবেন, এ তোমরা সইলেও আমি সইতে পারব না।’
জাহাঙ্গীরের মাতার প্রাণঢালা স্নেহ-আদরে তাহার কঠিন অভিমানের আবরণ টুটিয়া পড়িয়াছিল, তবু সে পরিপূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের কথা ভাবিতেই পারে নাই।
কিন্তু কী করিতে কী হইয়া গেল! কেন সে দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে কাঁদিয়া ফেলিল।
মোমি ব্যতীত তখনও কেহ জাগিয়া উঠে নাই। তহমিনা উঠিতে গিয়াও যেন উঠিতে পারিল না। তাহার বুকে-শরীরে ভীষণ ব্যথা। শুইয়া শুইয়াই দেখিল, জাহাঙ্গীরের মাতা তাহাদের ঘরের দাওয়ায় মাটিতে বসিয়া পড়িয়া কোরান ‘তেলাওত’ করিতেছেন।
অপূর্ব ভক্তি-মধুর সে কণ্ঠস্বর! তাহার এক বর্ণও সে বুঝিতে পারিতেছিল না। কিন্তু কেমন এক অজানা শ্রদ্ধায় তাহার মন ভরিয়া উঠিল। তাহার মনের অর্ধেক গ্লানি যেন কাটিয়া গেল।
সে চেষ্টা করিয়া উঠিয়া পড়িল।
জাহাঙ্গীরের মাতা কোরান তুলিয়া রাখিয়া বলিলেন, ‘উঠেছ মা সোনা! এ কী? তোমার চোখ মুখ অমন হয়ে গেছে কেন মা? অসুখ করেছে বুঝি?’
তহমিনার মনে হইল, তাহাকে দেখিয়াই বোধ হয় মাতা সব বুঝিতে পারিয়াছেন। সে লজ্জায় অধোবদন হইয়া বলিল, ‘জি, না।’
জাহাঙ্গীরের মাতা তাহাকে বক্ষে টানিয়া ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন, ‘বালাই! এমন বদ-খেয়ালি কথা আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায় মা। – তোমার মা কখন উঠবেন? তাঁহাকে যে দেখলুমই না!’
তহমিনার কিছু বলিবার আগেই মোমি বলিয়া উঠিল, ‘মা যে পাগল। মা উঠলেই তো কাঁদতে শুরু করবে বড়ো ভাইয়ের নাম করে!’
জাহাঙ্গীরের মাতা সব শুনিয়াছিলেন। তাঁহার চক্ষে জল আসিল। মোমিকে বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন, ‘তোমার মা ভালো হয়ে যাবেন মা। আমরা তোমার মাকে কলকাতা নিয়ে গিয়ে ডাক্তার দেখাব। আর, যদ্দিন তোমার মা ভালো হয়ে না উঠেন, তদ্দিন আমি হব তোমার মা, কেমন?’
কলিকাতা যাওয়ার কথায় মোমি অত্যন্ত খুশি হইয়া উঠিল। সে কলিকাতা সম্বন্ধে তাহার দাদাভাই-এর কাছে কিছু কিছু গল্প শুনিয়াছিল। সে কলকাতা সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করিতে লাগিল। জাহাঙ্গীরের মাতা হাসিয়া সে সবের উত্তর দিতে লাগিলেন।
অল্পক্ষণের মধ্যেই সকলে জাগিয়া উঠিল। গ্রামে বেগম আসিয়াছে বলিয়া হইচই পড়িয়া গেল। ঘরে মেয়েদের ভিড় লাগিয়া গেল।
জাহাঙ্গীরের মাতা বা দেওয়ান সাহেব বিবাহের কোনো কথাই তুলিলেন না।
জাহাঙ্গীরের মাতা হারুণের পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ‘আপনার কাছে একটা ভিক্ষা চাইতে এসেছি! অবশ্য ছেলের বন্ধুর বাড়ি দেখতে আসাও আমাদের এখানে আসার আর একটা কারণ। আমি পশ্চিমবঙ্গের পল্লিগ্রাম কখনও দেখিনি – এই অবসরে তাও দেখা হয়ে গেল।’
হারুণের পিতা বিনয়কুণ্ঠিতস্বরে বলিলেন, ‘আপনারদের মতো লোক যে গরিবের বাড়ি এসেছেন, এই আমার পরম সৌভাগ্য। জাহাঙ্গীর বাবাজি না এলে তো আপনার পদার্পণ হত না এ অজ-পাড়াগাঁয়ে। – আর আপনাকে ভিক্ষা দেওয়ার মতো কোনো কিছুই নেই আমার।’
জাহাঙ্গীরের মাতা বলিলেন, ‘আপনার যে সন্তান-রত্ন আছে – তারাই যে সাত রাজার ধন। আমি হারুণকে ভিক্ষা চাচ্ছি। সে আমার নতুন জমিদারি স্টেটের ম্যানেজার হবে। আপাতত সে মাসে তিনশো টাকা করে পাবে। আমার একটি মাত্র ছেলে, কিন্তু সে কিছু নেয়ও না, দেখেও না। সে এরই মধ্যে আধা-দরবেশ হয়ে গেছে। হারুণ কিন্তু আমার ছেলের মতোই থাকবে – আর তার সাথে সাথে আপনাদেরও কলকাতা যেতে হবে। হারুণের কাছেই আপনারা থাকবেন। হয়তো চিকিৎসা হলে ওর মাও ভালো হয়ে উঠতে পারে!’
হারুণের পিতা বহুক্ষণ কোনো কথা বলিতে পারিলেন না। তবে কি ভূণীকে পুত্রবধূ করিতে পারিবেন না বলিয়া তাঁহার এই জমিদারি চাল? ইহা কি তাহারই ক্ষতিপূরণ? তাঁহার আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল। ক্ষুণ্ণস্বরে তিনি বলিলেন, ‘আপনার দয়ার জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ দিচ্ছি বেগম সাহেবা, কিন্তু হারুণের তিনশো টাকা মাইনে পাবার মতো তো গুণ বা কর্মক্ষমতা নাই। আপনিও আমার ছেলের বন্ধুর জননী কাজেই আত্মীয়াও বললে হয়। আমাদের খুবই অভাব, তবু মাফ করবেন – আপনার কাছ থেকে এ দান নিতে আমার হাত উঠবে না।’
দেওয়ান সাহেব বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, ‘বেগম সাহেবাকে আত্মীয়ার মতোই বলছেন কেন খোন্দকার সাহেব, উনি তো আপনার বড়ো আত্মীয় হতে চলেছেন – দু দিন পরে বেয়ান হবেন – ওঁকে যদি এমন করে ফিরিয়ে দেন, আমরা সকলে বড়ো ব্যথা পাব। এখানে আজ সকালে গ্রামের লোকের মুখে শুনেছি আপনাদের বাড়িতে কোনো ভিখারি সোনা-রূপা না পেয়ে ফিরে যেত না। আমরাই কি তা হলে শুধুহাতে ফিরে যাব?’
হারুণের পিতা এইবার গলিয়া গিয়া বেদনার্ত কণ্ঠে বলিলেন, ‘সেদিন তো আমাদের নাই দেওয়ান সাহেব! এখন এক মুঠো চাউল দিতে পারিনে ভিখিরিকে। আমার ওয়ালেদ সাহেব পর্যন্ত সত্যই আমাদের বাড়ির এই রেওয়াজ ছিল। আমিও তা দেখেছি মাত্র, কিন্তু এ কমবখ্ত বাপ-দাদার সে ট্র্যাডিশন বজায় রাখতে পারেনি!’
জাহাঙ্গীরের মাতা বলিয়া উঠিলেন, ‘হারুণ আর তহমিনাই তো আপনার সোনার চেয়েও অমূল্য রত্ন – আমরা ওই সোনাই তো চাচ্ছি!’
হারুণের পিতা বিচলিত হইয়া উঠিলেন, ‘আর আমায় লজ্জা দেবেন না, দোহাই! গোস্তাখীর যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছেন। আমি আপনাদের যে ধরনের ধনী মনে করেছিলুম – আপনারা তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বাইরের ঐশ্বর্য আপনাদের অন্তরের ঐশ্বর্যকে দেখছি এতটুকু মলিন করতে পারেনি। ভিক্ষা ভিক্ষা বলবেন না, ওরা আজ থেকে আপনারই সন্তান হল। আমি তো থেকেও নাই। আমি অন্ধ হয়ে ওদের কোনো-কিছুই দেখতে পারিনে। বাপ অন্ধ, মা পাগল। ওদের তো বাপ-মা থেকেও নেই! এখন থেকে আপনারাই ওদের বাপ-মা হলেন। এখন আমি শান্তিতে মরতে পারব।’ বলিতে বলিতে তাঁহার কণ্ঠ ভাঙিয়া আসিল, আর বলিতে পারিলেন না।
দেওয়ান সাহেব বলিলেন, ‘শুধু ওদের তো নিতে আসিনি, আপনাদের সকলকেই যে নিতে এসেছি। আপনার পৈতৃক ভিটে চিরদিনের জন্য ছেড়ে যেতে বলছিনে, কিছুদিন কলকাতা থেকে আপনাদের দুই জনারই চিকিৎসাপত্র করান – খোদা যদি ভালো করে তোলেন আপনারা আবার ফিরে আসবেন এই বাড়িতে!’
হারুণের পিতা আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, ‘ভূণীর শাদি কি তা হলে কলকাতাতেই সম্পন্ন করতে চান? কিন্তু, তা তো হতে পারে না সাহেব।’
অনেক তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল, বিবাহ গ্রামেই হইবে! কিন্তু কিছুদিনের জন্য সেটা স্থগিত রহিল। হারুণ ইতিমধ্যে তাহার এই পুরাতন বাড়ির সংস্কার করিবে। হারুণের পরীক্ষা দেওয়া পর্যন্ত হারুণের পিতা হারুণের জমিদারি কার্যে সাহায্য করিবেন। কথা হইল, এখন গ্রামের কাহাকেও বিবাহ সম্বন্ধে কিছু বলা হইবে না। হারুণ জমিদারি স্টেটে চাকুরি লইয়া সপরিবার কিছুদিনের জন্য চলিয়া যাইতেছে – ইহাই সকলকে জানানো হইবে। ইহাও স্থির হইল, আর তিন দিনের মধ্যে সমস্ত ঠিকঠাক করিয়া যাত্রা করিতে হইবে।
হারুণের পিতা ভয় করিয়াছিলেন, ইহাতে হয়তো একমাত্র ভূণীরই আপত্তি হইবে। কারণ কাল পর্যন্ত সে নাগিনির মতো ফণা ধরিয়াছে। কিন্তু ভূণীকে সব কথা বলার পর সে যখন এতটুকুও আপত্তি উত্থাপন করিল না – তখন পিতা বিস্মিত হইয়া ইহার কারণ সন্ধান করিতে গিয়া মনে মনে হাসিলেন। ভাবিলেন ‘বেটির আমার বর চোখে ধরেছে কিনা, তাই আর কথাটি কইতে পারলে না!’
হারুণের মাতা কিন্তু জাগিয়া উঠিয়া হইচই করিয়া তুলিলেন। এইসব অজানা লোকজন দেখিয়া কখনও তিনি হাসিতে, কখনও বা তারস্বরে মিনাকে ডাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মায়ের ডাকে জাহাঙ্গীর ভিতরে আসিতেই উন্মাদিনী ‘ওই আমার মিনা এসেছে, আয়, আয়, সাইকেল দেব’ বলিয়া জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কিছুতেই ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন না। মাতার আদেশে জাহাঙ্গীর সেইখানে অপরাধীর মতো বসিয়া রহিল।
সে আর চোখ তুলিয়া কাহারও পানে চাহিতে পারিল না! সব চেয়ে মুশকিল হইল ভূণীর, সে বাহির হইতে পারে না, অথচ বাহির না হইলেও নয়।
লজ্জায় মাথা খাইয়া ভূণীকে দুই একবার বাহিরে আসিতে হইল। সে না আসিলে চলিবেই বা কী করিয়া? এত লোকের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা তো তাহাকেই করিতে হইবে।
জাহাঙ্গীরের মাতা হারুণের মাতাকে অনেক বুঝাইয়া জাহাঙ্গীরকে বাহিরে পাঠাইয়া দিয়া তহমিনাকে লইয়া পড়িলেন। রান্নার সমস্ত ব্যাপার তাঁহার বাঁদিদের হাতে তুলিয়া দিয়া তিনি ভূণীকে স্নান করাইয়া যখন হিরা-জহরত বসন-ভূষণে সাজাইয়া তুলিলেন, তখন গ্রামের মেয়েরাই বলিল, ভূণীর যে এত রূপ – তাহা তাহারাও জানিত না। অলংকার ও কাপড়-চোপড়ের বাহার দেখিয়া সকলেই বলিল, মেয়ে বরাত লইয়া আসিয়াছিল বটে! কেহ কেহ ইহাও বলিল যে, অত গহনা-কাপড় দিয়া সাজাইলে তাহার মেয়েকেও ইহার চেয়ে কম সুন্দর দেখাইত না।
মোমি ও মোবারক তাহাদের অদৃষ্টপূর্ব বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া উঠিল। গ্রামের সমস্ত বাড়িতে সন্দেশ মিঠাই পরিবেশন করা হইল। সকলে এই সন্দেশ দেওয়ার অর্থ অন্যরূপ করিল। সন্দেশের মূলে যে ভূণী, ইহা লুকাইলেও কাহারও আর বুঝিতে বাকি থাকিল না।
দুই দিনেই দেওয়ান সাহেব ও জাহাঙ্গীরের মাতা গ্রামের প্রায় সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন তাঁহাদের সহজ সরল নিরহংকার ব্যবহারে।
গ্রামের আত্মীয়স্বজনের নিকট অশ্রুসিক্ত চোখে বিদায় লইয়া হারুণেরা তাহাদের পৈতৃক ভিটার মায়া কাটাইয়া কলিকাতা যাত্রা করিল।
হারুণের নিকট-আত্মীয় একজন তাহাদের বাড়ি দেখাশুনা করিবেন কথা থাকিল। ইতিমধ্যে হারুণ আসিয়া নতুন করিয়া বাড়ি তৈরি করিয়া যাইবার পর তাহার পিতা-মাতা ফিরিয়া আসিবেন বলিয়া আত্মীয়স্বজনকে আশ্বাস দিল।…
হারুণের মাতা জাহাঙ্গীরকে দেখা অবধি আর বেশি কান্নাকাটি করেন নাই। তাঁহাকে বিশ্বাস করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, তাঁহার মিনা বড়ো হইয়া বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। উন্মাদিনী তাহাই বিশ্বাস করিয়াছে। কাজেই তাঁহাকে লইয়া যাইতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই।
কুহেলিকা – ১৭
স্টেশনে পঁহুছিয়াই জাহাঙ্গীর দেখিল, সারা গায়ে ভস্ম-বিভূতি মাখা জটাজূটধারী এক পৌনে-ষোলো-আনা নাগা সন্ন্যাসী তাহার চিমটার ইঙ্গিতে তাহাকে যেন আহ্বান করিল।
জাহাঙ্গীর দেখিল সন্ন্যাসী ইঙ্গিত করিয়াই রেললাইনের অপর পারে এক বৃক্ষনিম্নে গিয়া বসিলেন। সেখানে আরও বহু সন্ন্যাসী – কেহ ধুনি জ্বালাইয়া, কেহ ধ্যান করিতেছে, কেহ গাঁজা টানিতেছে, কেহ ভজন-গান করিতেছে।
জাহাঙ্গীর কাহাকেও কিছু না বলিয়া সন্ন্যাসীর অনুসরণ করিল। জিনিসপত্র নামানোর হ্যাঙ্গামে কেহ অত লক্ষ করিল না।
সন্ন্যাসী দল হইতে কিছু দূরে একটু নিরালায় গিয়া সেই সন্ন্যাসী বলিল, ‘তুমি আমাকে চেন না। অবশ্য, আমি তোমায় চিনি। আমাদের অত্যন্ত বিপদ। আজ ভোরে তোমার প্রমতদা ও পিনাকীর মাসিমা অস্ত্রশস্ত্র সমেত ধরা পড়েছেন। তোমার গাড়িতে তুলে দেবেন বলে তাঁরা গোরুর গাড়িতে করে সেসব আনছিলেন, রাস্তায় পুলিশ পাকড়েছে। এ খবর পুলিশ বাইরে প্রকাশ হতে দেয়নি, অন্যান্য সকলকে ধর-পাকড়ের জন্য। মাসিমাকে বাঁচাতে গিয়ে প্রমত্তকে ধরা দিতে হয়েছে – আমরা সকলে পালিয়ে এসেছি। পুলিশদের দু-জন মারা গেছে আমাদের গুলিতে । তোমার উপর বজ্রপাণির আদেশ, মাসিমার মেয়ে চম্পাকে নিয়ে কলকাতায় আপাতত তোমাদের বাসায় রাখবে। তার পর দু-এক দিনের মধ্যে বজ্রপাণি লোক পাঠিয়ে তাকে নিয়ে যাবেন। চম্পাকে বোরখা পরিয়ে মুসলমান মেয়ে সাজিয়ে রেখেছি। সে একটু পরেই স্টেশনে আসবে – তুমি তাকে তোমাদের গাড়িতে তুলে নিয়ো। খুব সাবধানে কিন্তু, পুলিশ ভয়ানক কড়া পাহারা দিচ্ছে প্ল্যাটফর্ম। চম্পার সাথে এক বাক্স মালপত্র আছে। সাবধান! প্রাণ দিতে হয় দিয়ো, তবু সেসব যেন বেহাত না হয়। যাও!’ – বলিয়াই সন্ন্যাসী সেখানে বসিয়া গাঁজার কলিকায় দম দিতে দিতে চিৎকার করিয়া উঠিলেন, – ‘বোম কালী কালকাত্তাওয়ালি।’…
জাহাঙ্গীর চক্ষে যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিল। কিন্তু ভয় পাইলে চলিবে না, ভাবিবারও অবকাশ নাই। তাহাকে প্রাণ দিয়া কর্তব্য পালন করিতে হইবে। সে স্টেশনে আসিয়া দেখিল, জিনিসপত্র স্যালুনে উঠানো হইতেছে। গাড়ি আসিবার তখনও অনেক দেরি।
তাহার মাতা ভূণী মোমি প্রভৃতি স্যালুনে উঠিয়া বসিয়াছিলেন। স্যালুনটা প্ল্যাটফর্ম হইতে কিছু দূরে ছিল। সে দেখিল, আর একখানা পালকি তাহাদের স্যালুনের দিকে আসিতেছে। সে তাহার মাতাকে বলিল, ‘মা, বলতে ভুলে গেছি, আমাদের মউলবির ভাগনি আমাদের সাথে যাবে। দু-একদিন আমাদের বাড়িতে সে থাকবেও। ডায়াসেশান কলেজে সে পড়ে। মউলবি সাহেব বিশেষ কাজে আজ যেতে পারলেন না, উনি দু-এক দিনের মধ্যেই কলকাতা এসে পঁহুচবেন।’
বলিতে বলিতে পালকি আসিয়া স্যালুনের নিকট থামিল এবং একটি বোরখা-পরা তরুণী নামিয়া স্যালুনে উঠিয়া আসিল। আসিয়াই সে মুসলমানি কায়দায় জাহাঙ্গীরের মা-র পদধূলি লইল। বাঁদিরা তাহার বাক্স-প্যাঁটরা স্যালুনে তুলিয়া লইল। মাতা আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, ‘এবার বোরখাটা খুলে ফেলো মা, যা গরম সেদ্ধ হয়ে গেছ বুঝি।’
চম্পা সামনের খড়খড়ি ফেলিয়া দিয়া বোরখা খুলিয়া ফেলিল। তাহার রূপে সকলের চক্ষু যেন ঝলসিয়া গেল। ভূণীর মুখ ম্লান হইয়া গেল। সত্যসত্যই চম্পার কাছে তাহার রূপ নিষ্প্রভ হইয়া পড়িল।
বাঁদিরা বলিয়া উঠিল, ‘বিবিসাব, আপনার বাস্কে কী রাখছেন কন তো। পাতর রাখছেন না তো? মাইয়ো মা, যা ভারী!’
চম্পা হাসিয়া বলিল, ‘বই-পত্তর আছে কিনা, তাই অত ভারী!’
মা মুগ্ধনেত্রে তাহাকে দেখিতেছিলেন। দেখিতেছিলেন, এ রূপ নয়, রূপের শিখা। রূপের চেয়ে তেজ দীপ্তি আরও বেশি। চক্ষুতে অদ্ভুত জ্যোতি, তাকানো যায় না।
মা জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তোমার নামটা কী মা?’ চম্পা কিছু বলিবার আগেই জাহাঙ্গীর বলিল, ‘ওর নাম আমিনা।’
মাতা বলিলেন, ‘এঁর কথা তো তুই কখনও বলিসনি খোকা!’
জাহাঙ্গীর বলিল, ‘ওঁর কথা তো আমি আগে জানতুম না মা। আমি স্টেশনে আসতেই মউলবি সাহেব ওঁকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে আমাদের সাথে নিয়ে যাবার জন্য দিয়ে গেলেন। মউলবি সাহেব আমাদের সাথে সেদিন যেতে পারেননি বলে লজ্জায় আর তোমার সঙ্গে দেখা করলেন না। তা ছাড়া ওঁর কাজও ছিল।’
মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, ‘তোমার মার অসুখ করেছিল শুনেছিলুম, এখন তিনি ভালো আছেন তো?’
চম্পা ওরফে আমিনা বলিল, ‘জি হাঁ। মা চেঞ্জে যাবেন কাল, তাই আমি কলকাতা চলে যাচ্ছি। আমার পড়াশুনার ক্ষতি হবে বলে তাঁর সাথে গেলুম না। কয়দিন আপনাদের তকলিফ দেব।’
মা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, ‘ছি মা, ও কথা বলতে নেই। ও তোমার নিজের বাড়িই মনে করবে। হাঁ দেখো, তোমার সাথে মা পরিচয় করে দিতে ভুলে গেছি, এই হচ্ছে তহমিনা – আমার হবু-বউমা। এ হচ্ছে ওর ছোটো বোন মোমি, ইনি হচ্ছেন ওর মা – শরীর খারাপ তাই ঘুমোচ্ছেন।
চম্পা ভূণীর পাশে আসিয়া বসিল, কিন্তু তাহার মুখ যেন কেমন ম্লান হইয়া গেল। ভূণীর তাহা চক্ষু এড়াইল না। চম্পা ভূণীর সহিত ভাব করিবার চেষ্টা করিল। কিন্ত দুই জনে কেহই যেন সহজ হইতে পারিল না।
জাহাঙ্গীর বিস্ময়-বিমুগ্ধ নেত্রে চম্পার পানে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। অপূর্ব তাহার আত্মসংযম! আজই সকালে যে এত বড়ো দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে – তাহার কোনো দুর্ভাবনার ছায়া পর্যন্ত পড়ে নাই তাহার চোখে মুখে। ও যেন বহু পূর্ব হইতেই ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।
চম্পা হঠাৎ জাহাঙ্গীরের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, ‘বেশ লুকিয়ে লুকিয়ে বউ চুরি করতে এসেছিলেন তো! কাউকে এতটুকু জানতে দেননি!’ বলিয়াই জাহাঙ্গীরের মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, ‘মা হয়তো কী ভাবছেন! কলেজে পড়ে আমরা হয়তো বেহায়া হয়ে গেছি!’
মা হাসিয়া বলিলেন, ‘না মা! আমাদের বাড়িতেও পর্দার অত কড়াকড়ি নেই। তোমার মুখে বোরখা দেখে একটু বরং আশ্চর্য হয়ে গেছিলাম।’
চম্পা হাসিয়া বলিল, ‘কী করি মা, মামার জন্য আমায় বোরখা নিতে হয়েছিল, মামা একটু গোঁড়া!’
বলিয়াই ভূণীর পানে ফিরিয়া বলিল, ‘আমি কিন্তু তাই তোমায় “আপনি” বলতে পারব না, আর বউদি বলে ডাকব – কেমন? ভাবি-টাবির চেয়ে বউদি অনেক ভালো শোনায়।’
ভূণী এইবার হাসিয়া মুখের ঘোমটাটা বেশি করিয়া টানিয়া দিল।
এমন সময় ক্লান্ত হারুণ আসিয়া বলিল, ‘মা, সব জিনিসপত্র উঠে গেছে।’ মাতা তাহাকে গাড়িতে উঠিতে বলিয়া চম্পাকে বলিলেন, ‘এর বোধ হয় নাম শুনেছ আমিনা, এই আমাদের কবি হারুণ, তহমিনার বড়ো ভাই। আর হারুণ, ইনি আমিনা, তোমাদের প্রফেসর আজহার সাহেবের ভাগনি। আমাদের সাথে কলকাতা যাচ্ছেন। ডায়াসেশানে পড়েন।’
চম্পা আদাব করিয়া বলিল, ‘আপনার যথেষ্ট নাম শুনেছি। কিছু কিছু কবিতাও পড়েছি। চমৎকার লেখেন আপনি। আমার সৌভাগ্য যে, আপনার দেখা পেলুম।’
হারুন অভিভূতের মতো চম্পার পানে চাহিয়াছিল, সে যেন তাহার কল্পলোকের মানস-লক্ষ্মীকে স্বপ্নে দেখিতেছে! চম্পার এই প্রশংসায় তাহার মনে হইল, তাহার কবি-জীবন ধন্য হইয়া গেল। সে ইহার প্রত্যুত্তরে একটি কথাও বলিতে পারিল না, সমস্ত মুখ তার আরক্তিম হইয়া উঠিল।
ট্রেন আসিয়া পড়িল। তাহাদের স্যালুনকে টানিয়া ট্রেনের পশ্চাতে জুড়িয়া দিল। জাহাঙ্গীর দেখিল, জনকতক টিকটিকি তাহাদের কামরার সম্মুখ দিয়া কেবলই যাতায়াত করিতেছে।
জাহাঙ্গীর কিছু বলিবার আগেই দেওয়ান সাহেবের হুংকার শোনা গেল। তিনি নামিয়া তাহাদের এক তাড়া দিতেই তাহারা প্রার্থনা করিয়া চলিয়া গেল। গাড়ি ছাড়িয়া দিল।
জাহাঙ্গীর চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। আজিকার বিপদের ছায়া তাহার মুখে ঘন বেদনার ছাপ মারিয়া দিয়াছিল। সে ভাবিতে লাগিল, যে কোনো মুহূর্তে তাহার জীবন বিপন্ন হইতে পারে। বাথরুমে ঢুকিয়া সে তাহার পিস্তলটা পরীক্ষা করিয়া ভালো করিয়া তলপেটে কোঁচার নীচে সামলাইয়া রাখিল। আসিয়া চম্পাকে কী যেন ইঙ্গিত করিল, চম্পাও চক্ষু ইঙ্গিতে কী যেন বলিল। ভূণী ঘোমটার আড়াল হইতে তাহা দেখিতে পাইল। তাহার শরীর মন জ্বালা করিয়া উঠিল। ইহারা তাহা হইলে শুধু আজিকার পরিচিত নয়।
মাতা জাহাঙ্গীরের মুখ চোখ দেখিয়া বলিলেন, ‘খোকা, তোর মুখ চোখ অমন কালো হয়ে গেছে কেন? কিছু খাসনি বুঝি এখনও? তুই আর হারুণ কিছু খেয়ে নে তো। কী রকম মুখ চোখ বসে গেছে তোর !’
জাহাঙ্গীর বলিল, ‘না মা, খিদে পায়নি মোটেই, এমনি শরীরটা কেমন খারাপ লাগছে।’
মা বলিলেন, ‘শরীর খারাপ করেছে কেন রে? যা ছেলে তুই, কারুর কথা তো শুনবিনে। অতটা রাস্তা হেঁটে এলি, কিছুতেই পালকিতে চড়লিনে! দেখি’ – বলিয়া কপালে হাত দিয়া বলিলেন, ‘তোর গাও যে গরম হয়েছে খোকা! শুয়ে পড় শুয়ে পড় এইখানে।’
জাহাঙ্গীর শুইয়া পড়িল। গাড়ির সকলে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। চম্পা হাসিয়া বলিল, ‘ব্যস্ত হবেন না মা, নতুন দায়িত্ব ঘাড়ে নিচ্ছেন কিনা, তারই চিন্তায় ওঁর শরীর হয়তো একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।’
মা ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, ‘না মা, তুমি জান না, ওর শরীরের উপর একটুও যত্ন নেই, সত্যিই ওর শরীর খারাপ করেছে।’
চম্পা বলিল, ‘তা তো দেখেই বোধ হচ্ছে! ওঁর শরীরটা যেন সন্ন্যাসীর, যত রকমে পেরেছেন, ওকে নির্যাতন করেছেন। লক্ষ রাখবেন মা, সন্ন্যাসী-টন্ন্যাসী না হয়ে যান!’
মা হাসিয়া বলিলেন , ‘এবার যার উপর লক্ষ রাখার ভার পড়েছে – সেই দেখবে মা। আমি তো ওকে বাগে আনতে পারিনি – দেখি অন্য কেউ পারে কিনা।’
চম্পা ভূণীর কানে কানে বলিল, ‘তুমি বেশ ভালো ঘোড়সওয়ার তো বউদি? জোর লাগাম কশে রেখো। নইলে এ বেহেড ঘোড়া ছুটতে শুরু করলে আটকে আর রাখতে পারবে না।’
ভূণী জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, ‘যদি তোমার মতো কথার চাবুক থাকত হাতে ভাই, তা হলে হয়তো পারতুম। ও ঘোড়া হয়তো একা তুমিই বাগে আনতে পার।’
চম্পা রাম-চিমটি কাটিয়া বলিল, ‘এই ননদ-নাড়া শুরু হল তা হলে!’
ভূণী উঃ করিয়া শব্দ করিয়া বলিল, ‘তুমি দেখছি শূর্পণখা!’
চম্পা হাসিয়া বলিল, ‘আর উনি বুঝি রাবণ, তুমি সীতা?’
জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, ‘ওধারে রাম-লীলা শুরু হল, হারুণও কবিতার খাতা নিয়ে বসল, আমি ততক্ষণ কুম্ভকর্ণের ডিপুটিগিরি করি।’
বলিয়া চক্ষু বুজিয়া শুইয়া পড়িল। মাতা হাসিয়া পুত্রের ললাটে সস্নেহ কর সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।
কুহেলিকা – ১৮
গাড়ি বর্ধমানে আসিয়া পঁহুচিতেই কাহাদের চঞ্চল স-বুট পদশব্দে জাহাঙ্গীরের ঘুম ভাঙিয়া গেল। জাহাঙ্গীর উঠিয়া দেখিল, সকলে ঘুমাইয়া গিয়াছে। রাত্রি কতটা হইবে তাহা সে আন্দাজ করিতে পারিল না। কেবল হারুণ একাকী জাগিয়া এক মনে বোধ হয় কবিতা লিখিতেছে। একদল সশস্ত্র গোরা ও পুলিশ তাহাদের স্যালুন বারকতক প্রদক্ষিণ করিয়া স্যালুনের পূর্বের গাড়িটাতে উঠিয়া বসিল। ট্রেন ছাড়িয়া দিল।
জাহাঙ্গীরের বুঝিতে বাকি রহিল না – কোন বজ্র তাহার শির লক্ষ করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। সে কী করিবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। ধাক্কা দিয়া হারুণের ধ্যান ভঙ্গ করিয়া সে চুপি চুপি বলিল, ‘হারুণ, ভীষণ বিপদ! তোমায় একটা কাজ করতে হবে।’
হারুণ ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া জাহাঙ্গীরের মুখের পানে হাঁ করিয়া তাকাইয়া রহিল। সে জাহাঙ্গীরের এই অহেতুক ভীতির কোনো কারণ খুঁজিয়া পাইল না।
জাহাঙ্গীর বলিল, ‘অনেকগুলো গোরা আর পুলিশ আমাদের গাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়া-আাসা করছিল, দেখেছ?’
হারুণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, ‘হাঁ!’
জাহাঙ্গীর বলিল, ‘ওরা খুব সম্ভব আমায় অ্যারেস্ট করবে। হয়তো আমাদের গাড়িও সার্চ করবে। সার্চ যদি করে – তা হলে আমরা সকলেই ভীষণ বিপদে পড়ব। তোমাকে সব কথা খুলে বলি, যাকে আমিনা বলে ভেবেছ – সে আমিনা নয় – আমাদের বিপ্লবীদলের একটি মেয়ে। ওর কাছে অনেক অস্ত্রশস্ত্র আছে। এরা সকলেই ঘুমুচ্ছে – এই অবসরে আমি আর ওই আমিনা নেমে পড়ব স্টেশনে। তুমি আস্তে আস্তে ওর বাক্সটা নামিয়ে দেবে। কোনো ভয় কোরো না। মাকে ভাবতে মানা কোরো – আমি কালই মোটরে করে বাড়ি পঁহুচিব তোমাদের সাথে সাথে।’
হারুণ বোবার মতো বসিয়া রহিল। মনে হইল, তাহার বাক্শক্তি রহিত হইয়া গিয়াছে। ‘মাকে বলো – আমিনার মামা তার করায় বর্ধমান স্টেশনে তা পেয়ে আমি তাঁকে আবার অণ্ডাল পৌঁছে দিতে যাচ্ছি – তার মায়ের ভয়ানক অসুখ বেড়েছে। অণ্ডাল থেকে তার মামা এসে নিয়ে যাবেন।’
বলিয়াই সে আস্তে ধাক্কা দিয়া চম্পাকে জাগাইল। চম্পাকে কোড-ওয়ার্ডে কী কথা বলিতেই সে লাফাইয়া উঠিয়া তাহার বুকের নীচে কী পরীক্ষা করিয়া দেখিল।
তাহার পর বাক্স দুইটি আস্তে আস্তে দোরগোড়ায় টানিয়া দরজা খুলিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিল। জাহাঙ্গীর আবার তাহাকে কী বলিতে সে তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকিয়া হিন্দু-সধবার বেশে সাজিয়া বাহির হইয়া আসিল। জাহাঙ্গীরও তাড়াতাড়ি ইউরোপিয়ান বেশে সজ্জিত হইয়া লইল। ইত্যবসরে ট্রেন শক্তিগড়ে একটু দাঁড়াইয়াই ছাড়িবার উপক্রম করিতে তাহারা ধীরে দুই জনে দুইটা বাক্স লইয়া নামিয়া পড়িল। জাহাঙ্গীর চাহিয়া দেখিল, সৌভাগ্যক্রমে গোরা বা পুলিশের কেহ সেদিকে লক্ষ করিল না। তাহারা ইহাদের কলিকাতায় পাকড়াও করিবে বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া হয়তো শুইয়াছিল।
হারুণ তেমনি পাথরের মতো বসিয়া রহিল। তাহার বাক্শক্তি এবং নড়িবার শক্তি দু-ই যেন কে হরণ করিয়া লইয়াছে।
জাহাঙ্গীর ও চম্পা বিপরীত দিককার প্ল্যাটফর্মে গিয়া দাঁড়াইতে বর্ধমান যাইবার ট্রেন আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন টিকিট করিবার সময় ছিল না। চম্পাকে একখানা শূন্য ফার্স্টক্লাসে তুলিয়া দিয়া সে গার্ডকে বলিয়া আসিল।
ট্রেন ছাড়িয়া দিল। চম্পা বলিল, ‘বর্ধমানে নামা হবে না। সেখানে পুলিশে নিশ্চয়ই কড়া পাহারা দিচ্ছে।’ স্থির হইল তাহারা রানিগঞ্জে নামিয়া সেখান হইতে ট্যাক্সি করিয়া কলিকাতা আসিবে। তাহা হইলে ধরা পড়িবার সম্ভাবনা থাকিবে না।
জাহাঙ্গীর ক্লান্ত হইয়া শুইয়া পড়িল। চম্পা বলিল, ‘দাদা তোমার মাথাটা টিপে দেব?’ জাহাঙ্গীর আপত্তি করিল না। চম্পা তাহার চম্পক আঙ্গুলি দিয়া জাহাঙ্গীরের কপাল টিপিয়া দিতে দিতে বলিল, ‘দাদা তোমার মা হয়তো এতক্ষণ কী মনে করেছেন!’
জাহাঙ্গীর হাসিয়া বলিল, ‘হ্যাঁ, মা হয়তো মনে করছেন, ছেলে আমার মেয়েটাকে নিয়ে উধাও হল।’
চম্পা জাহাঙ্গীরের হাতে চিমটি কাটিয়া বলিল, ‘যাও তুমি ভয়ানক দুষ্টু। আমাদের ও কথা বলতে নেই।’
জাহাঙ্গীর গম্ভীর হইয়া বলিল, ‘সত্যি তাই। আমাদের যে মন্ত্রে দীক্ষা, তাতে কেউ পুরুষ-নারী বলে নেই। সেখানে সকলে অগ্নি-সখা। তা নইলে তোমার মতো রূপে-গুণে অপরূপাকে কি এত কাছে পেয়ে নিজেকে বিশ্বাস করতে পারতুম?’
চম্পা বলিল, ‘সত্যি তোমার সে রকম দুর্বলতা আসতে পারে বলে তুমি ভয় কর?’
জাহাঙ্গীর উঠিয়া বসিয়া কহিল, ‘করি চম্পা। আমি আমাকে যত বেশি জানি, তুমি তো তা জান না।’
চম্পা ভয়ের ভান করিয়া বলিল, ‘তবে তোমার সঙ্গে আসা আমার উচিত হয়নি। অথচ প্রমতদা যাবার সময় আমায় তোমায় ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করতে মানা করেছিলেন। তুমি নাকি নারী জাতিটাকে ঘৃণা কর।’
জাহাঙ্গীর বলিল, ‘কতকটা তাই। ওদের বিশ্বাস করি না – শ্রদ্ধা করি না বলেই আমার অত ভয়। যাকে শ্রদ্ধা করি না, তার অসম্মান করতে আমার বাধবে না।’
চম্পা প্রশ্ন করিল, ‘এই যদি তোমার মনের ভাব তা হলে বিয়ে করতে যাচ্ছ কেন এক নারীকেই?’
জাহাঙ্গীর বলিল, ‘বিয়ে করব কি-না জানিনে চম্পা, কিন্তু তার সর্বনাশের আর কিছু বাকি রাখিনি।’
হঠাৎ সাপ দেখিলে লোক যেমন চমকিয়া উঠে, চম্পা তেমনই চমকিয়া উঠিয়া বলিল, ‘এ তুমি কী বলছ দাদা? হয় তুমি মিথ্যা কথা বলছ – কিংবা পাগল হয়েছে।’
জাহাঙ্গীর তেমনই স্থির কণ্ঠে কহিল, ‘আমি মিথ্যাও বলিনি, পাগলও হইনি চম্পা। এর পরে তোমার সাথেও হয়তো আর আমার দেখা হবে না। এই পৃথিবীর অন্তত একজন আমার বেদনার কাহিনি শুনে রাখুক – কী অভিশপ্ত জীবন নিয়ে আমি এসেছিলুম – কী হতে পারতুম অথচ কী হলুম।’
চম্পা কণ্ঠে বেদনা ও মিনতি ঢালিয়া দিয়া কহিল, ‘দাদা তুমি একটু শুয়ে ঘুমোও দেখি। আমি জেগে থেকে রানিগঞ্জে ট্রেন এলেই উঠিয়ে দেব। তোমার কিচ্ছু আমি জানতে চাইনে। কী হবে আমার জেনে? তোমায় দেখেছি, শ্রদ্ধা করেছি – শুধু এইটুকুই আমার যথেষ্ট।’
জাহাঙ্গীর বাধা দিয়া বলিল, ‘ না চম্পা, তোমাকে শুনতেই হবে। আমি এতদিন ভেঙে পড়িনি বা উচ্ছন্নে যাইনি প্রমতদা ছিলেন বলে। এখন আর আমার ভয় নাই। হয় স্বর্গারোহণ করব – নয় একেবারে যে পাঁক থেকে আমি উঠেছি সেই পাঁকেই ডুবে যাব।’
চম্পা প্রতিবাদের স্বরে বলিল, ‘তুমি পাঁক থেকে উঠতে পার না – যদি তা শুনেও থাক তা মিথ্যা।’
জাহাঙ্গীর ম্লান হাসিয়া বলিল, ‘তুমি হয়তো আমাকে পদ্মফুল মনে করছ – তা নাকি গোবরেও ফোটে চম্পা। কিন্তু আমি যে আমাকে পরীক্ষা করে দেখেছি। তুমি শুনে আশ্চর্য হবে – সে পরীক্ষায় আমি আমার মূলের পাঁককে দেখতে পেয়েছি। আর সে পাঁক অন্যের গায়েও গিয়ে লেগেছে।’
চম্পা কী ভাবিল। তাহার পর বলিল, ‘তুমি কি ভূণীর কথা বলছ? সত্যিই কি তুমি তার ক্ষতি করেছ?’
জাহাঙ্গীর উত্তেজিত হইয়া বলিল, ‘শুধু ক্ষতি চম্পা, যে ক্ষতির চেয়ে বড়ো ক্ষতি মেয়েলোকের হতে পারে না, আমি তার সেই ক্ষতি করেছি। এক মুহূর্তের দুর্বলতাকে জয় করে উঠতে পারলাম না।’
জাহাঙ্গীরের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। সে তাহা গোপন করিবার চেষ্টা না করিয়া বলিতে লাগিল, ‘তার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত তাকে বিয়ে করা। কিন্তু সে তো জানে না – আমি আমার পিতার কামজ সন্তান, – আমার মা কলকাতার এক বিখ্যাত বাইজি! একথা জানলে সে কি আর আমায় শ্রদ্ধা করতে পারবে? আমার মূলে যদি পাঁক না থাকত, তা হলে আমি অত বড়ো পাপ করতে পারতাম? আমার প্রতি রক্ত-কণিকায় যে ভোগী পিতা বেঁচে রয়েছে – আমি ভুললেও সে আমায় যে কেবলই নরকের দিকে টানবে চম্পা! এত ঐশ্বর্য, মা যা-ই হোন তাঁর এত স্নেহ – এই নিয়ে আর যে কেউ হয়তো পরম সুখে দিনাতিপাত করতে পারত। আমি কিন্তু পিতা-মাতার অপরাধ সহস্র চেষ্টা করেও অন্তর থেকে ক্ষমা করতে পারলুম না। অগ্মিমন্ত্রে দীক্ষা নিলুম – ভাবলুম, আগুনে পুড়ে হয় খাঁটি হব – নয় পুড়ে ছাই হব। খাঁটি হতে পারলুম না, এখন ছাই হওয়া ছাড়া আর আমার এ জন্ম থেকে মুক্তি নেই।’ জাহাঙ্গীর হাঁপাইতে লাগিল।
আশ্চর্য! চম্পা ঘৃণায় সরিয়া গেল না। অধিকন্তু অধিকতর স্নেহে তাহার কপালের রুক্ষ চুলগুলো সরাইতে সরাইতে বলিল, ‘লক্ষ্মীটি, চুপ করে শোও। তুমিও তো রক্ত-মাংসেরই মানুষ ভুল বড়ো বড়ো মহাপুরুষও করেন। যাঁদের জন্মে কোনো কলঙ্ক স্পর্শ করেনি, তাঁরাও তো সারা জীবন পাপে ডুবে রয়েছেন দেখছি। তোমাদের অগ্নিপন্থী দলেরই নামকরা দু-চার জনকে জানি, যারা আমার সর্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছিল। আমি ইচ্ছা করলে তাদের সর্বনাশ করতে পারতাম – করিনি, ক্ষমা করেছি। বিশেষ করে, তোমাদের অগ্নিপন্থীদের মনে যে ভীষণ পশু রয়েছে – তারই প্রেরণায় তোমরা হত্যা করতেও ভয় পাও না। সেই পশু শুধু হত্যার জন্যই নয় – অন্য কারণেও তো জেগে উঠতে পারে। তোমাদের মনের পশুকে একেবারে মেরে ফেললে তোমাদের দেবত্ব বা মনুষ্যত্ব দিয়ে আর যাই হোক – আমাদের যে মন্ত্র, যে সাধনা তার কিছু হবে না।’
জাহাঙ্গীর উঠিয়া বসিয়া চম্পার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, ‘ চম্পা, এমন কথা তো কেউ কোনোদিন বলেনি! প্রমতদাও না।’
চম্পা বাধা দিল না তেমনিভাবে বলিতে লাগিল, ‘তবু তুমি সত্যব্রতী। তোমরা পশুকে মানুষের চামড়া পরিয়ে লুকিয়ে রাখতে জান না। অন্য যাঁদের দেখেছি, তাঁরা সমস্ত বড়ো কর্মী ত্যাগী বীরপুরুষ, কিন্তু এই সত্যটুকু স্বীকার তাঁরা করেননি। তাঁদের দুর্বলতাকে নেপোলিয়নের লাম্পট্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন।’ যদিও আমি বিশ্বাস করি না – নেপোলিয়ন সেরকম ছিল।’
জাহাঙ্গীর চম্পার সেই তেজোব্যঞ্জক অপরূপ রূপমাধুরী দেখিতে দেখিতে উন্মত্ত হইয়া উঠিল। সে চম্পাকে সহসা বুকে চাপিয়া আর্তস্বরে বলিয়া উঠিল, ‘চম্পা, চম্পা! আমায় বাঁচাও! হয় আমায় একেবারে রসাতলে – যে পাঁক থেকে উঠেছি সেই পাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দাও, নয় আমায় ঊর্ধ্বে নিয়ে চলো হাত ধরে।’
চম্পা রহস্য-ভরা হাসি হাসিয়া বলিল, ‘তোমায় বাধা দেব না। জানি আগুনের তৃষ্ণা কত প্রবল। কিন্তু কী হবে এ করে? আমার পিনাকীদা গেছে, মা গেছেন, প্রমতদাও গেছেন। আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, বজ্রপাণির দলের হয়তো একজনও আর বাইরে নেই। আমি আজ তোমার কাছে আত্মসমর্পণ না করি, কাল করতে হবে। কারণ, তুমি ছাড়া পৃথিবীতে আমার তো আর কোনো অবলম্বনই নাই। আমিও তো রক্ত-মাংসের মানুষ – আর তোমাদেরই মতো পশুত্ব দিয়ে পশুকে জয় করার সাধনা আমার। লোভ তৃষ্ণা তোমাদের কারুর চেয়ে আমার কম নেই। কিন্তু, এর যে একটামাত্র পথ খোলা ছিল – সে পথও তো তুমিই বন্ধ করেছ!… তোমার মায়ের টাকা আছে, তুমি হয়তো বেঁচে গেলেও যেতে পার – কিন্তু তাতে আমার কী? আমি কি তোমার দেবদাসী হয়ে থাকব? জাত ধর্ম আমি মানিনে, সে শিক্ষাই পাইনি জীবনে। কিন্তু আমার নারী ধর্ম তো আছে। তাকে আজ যদি বিসর্জন দিই, কাল তুমি আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে – যেমন করে ভূণীকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছ! তোমাকে বলতে আমার লজ্জা নেই – তোমাকে দেখেই আমার ভালো লেগেছিল। তরুণ অরুণের মতো যেদিন তুমি এসে আমাদের আঙিনায় দাঁড়িয়েছিলে তোমার প্রখর দীপ্তি নিয়ে – সেইদিন থেকে তোমায় সকল প্রাণ মন দিয়ে শ্রদ্ধা করে আসছি। মরণোন্মুখ তৃষ্ণাতুর তুমি এসে দাঁড়িয়েছ – তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই – তবু ওইটুকুর বিনিময়ে আমার এমন অমূল্য শ্রদ্ধাটুকু কেড়ে নিয়ো না। তুমি ভূণীকে বিয়ে করে সুখী হও, আমি তোমাদের ভগিনীর স্নেহে সেবা করব, – যত্ন করব, তার পর মা যদি ফেরেন – মার কোলে ফিরে যাব!…’ চম্পা সহসা কাঁদিয়া ফেলিল!
জাহাঙ্গীর চম্পাকে বুকের আরও কাছে টানিয়া লইয়া আদরে অভিষিক্ত করিয়া সান্ত্বনা দিতে দিতে বলিতে লাগিল, ‘তুমি ঠিকই বলেছ চম্পা। আগুনের আকুল তিয়াসা তো মিটবার নয়। তৃষ্ণা কেবল বেড়েই চলবে? পশুর পশু-জন্ম সার্থক হয় দেবীর বেদিতলে তার বলিদান হয়ে গেলে।… জীবনে কাউকে ভালোবাসিনি, কারুর ভালোবাসা পাইনি, আজ তাও যখন পেয়ে গেলুম দৈববলে – তখন তো আমি বেঁচে গেলুম।… আমি আমার কর্তব্য ঠিক করে ফেলেছি চম্পা, তোমাকে মার হাতে সঁপে দিয়ে – যে তুফান উঠেছে তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ব প্রমতদার মতো।… আমার যে ঐশ্বর্য রইল – তাতে তোমাদের এ জীবনে শান্তি ছাড়া আর কোনো কিছুর অভাব হবে না। আমি আমার সকল ঐশ্বর্য তোমায় দিয়ে যাব। তুমি আমার হয়ে ওই ঐশ্বর্য দেশ-জননীর দুঃখী সন্তান আর ভাই-বোনদের বিলিয়ে দিয়ো।’
চম্পা দুই হাতে জাহাঙ্গীরকে জড়াইয়া বালিকার মতো কাঁদিতে লাগিল। হঠাৎ যেন পাহাড় ফাটিয়া ঝরনা ধারার বাঁধ টুটিয়া গিয়াছে।
জাহাঙ্গীর ধীর শান্তস্বরে বলিতে লাগিল, ‘আমি জীবনে ভাবিনি – নারীজাতিকে কখনও শ্রদ্ধা করতে পারব – তাদের ভালোবাসতে পারব – তাদের প্রেমে বিশ্বাস করব।…. আজ আমার কাছে এই পাপের পৃথিবীও সুন্দর হয়ে উঠেছে। আমার মরুভূমির ঊর্ধ্বে মেঘের স্বপন ভেসে উঠেছে! ফুল ফুটল না সে মরুভূমিতে – দুঃখ করিনে তার জন্য। আমার চিরদগ্ধ বুক তো শীতল হল।’
সূর্যমুখী যেমন করিয়া অস্ত-সূর্যের পানে চায়, তেমনি করিয়া মুখ তুলিয়া চম্পা বলিল, ‘তোমার ঐশ্বর্যের অভিশাপ আমায় দিয়ে যেয়ো না, ও আমি সহ্য করতে পারব না। সবাই তো আমায় ছেড়ে গেল, তুমি যেয়ো না।’
জাহাঙ্গীর চম্পার চক্ষু মুছাইয়া দিতে দিতে বলিল, ‘তোমাকে তো দিয়ে যাব না ওসব চম্পা। আমার মতো যেসব যুবক দেশ-জননীর পায়ে আত্মবলি দিয়ে তাদের আত্মীয়স্বজনকে অকূল পাথারে ভাসিয়ে গেল, তাদের নিরন্ন মুখে দু-মুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার ব্রত হবে তোমার। তুমি হবে তাদের দেবী অন্নপূর্ণা।’
ট্রেন একটি স্টেশনে থামিতেই চম্পা বাহিরে মুখ বাড়াইয়া বলিয়া উঠি, ‘ওঠো ওঠো, রানিগঞ্জে এসে পৌঁচেছি। মাত্র দু-মিনিট স্টপেজ।’
নামিয়া ট্যাক্সি ঠিক করিতে আরও আধ ঘণ্টা কটিয়া গেল। যখন তাহারা যাত্রা করিল, তখন রাত্রি দুইটা।
মোটর চলিতে আরম্ভ করিলে জাহাঙ্গীর এলাইয়া পড়িয়া বলিল, ‘আমার কী মনে হচ্ছে চম্পা, জান? যেন এ পথের আর শেষ না হয়! যুগ-যুগান্তর ধরে শুধু তোমায় পাশে নিয়ে এমনি করে ছুটে চলি।’
চম্পা কথা কহিল না। চক্ষু বুজিয়া কী যেন ভাবিতেছিল। কেহ আর কোনো কথা কহিল না। গাড়ি উল্কাবেগে ছুটিতে লাগিল, মোটর হাওড়া ব্রিজের মোড়ে আসিতেই হঠাৎ চার পাঁচজন সার্জেন্ট গাড়ি আগুলিয়া দাঁড়াইয়া মোটর থামাইবার আদেশ করিল।
জাহাঙ্গীর ও চম্পা জ্যা-ছিন্ন ধনুকের মতো সোজা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। সশস্ত্র সার্জেন্ট-দল রিভলবার হাতে লইয়া গাড়িতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। জাহাঙ্গীর পিস্তল ছুড়িতে একজন সার্জেন্ট মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। অন্য সার্জেন্ট জাহাঙ্গীরকে ধরিয়া ফেলিল।
এই ধস্তাধস্তির ফলে চম্পা কখন সরিয়া পড়িয়াছিল, কেহ টের পাইল না।
দুই তিনজন সার্জেন্ট ওই ট্যাক্সি লইয়া দুই তিন দিকে তাহার খোঁজে ধাওয়া করিল।
কুহেলিকা – ১৯
এদিকে জাহাঙ্গীরের মাতা হাওড়া স্টেশনে পঁহুছিয়া জাহাঙ্গীর ও চম্পাকে দেখিতে না পাইয়া এবং হারুণের কাছে সমস্ত শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। ভূণীর মুখে কে যেন কালি ঢালিয়া দিল।
হারুণ কিন্তু যে ভয় করিতেছিল, তাহার কিছুই হইল না। কেহ তাহাদের গাড়ি সার্চ করিল না। হারুণ দেখিল, প্ল্যাটফর্ম মিলিটারি পুলিশে ও গোরায় ছাইয়া ফেলিয়াছে। কয়েকজন যুবককে ধরিয়া তাহারা প্রিজনার-ভ্যানে পুরিল, তাহাও সে দেখিল। ভয়ে তাহার মুখ কাগজের মতো সাদা হইয়া গেল।
সে দেখিল ধৃত বন্দিদের মধ্যে জাহাঙ্গীর নাই। সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।
হারুণ জাহাঙ্গীরের মাতাকে জাহাঙ্গীরের উপদেশ মতোই সব কথা বলিয়াছিল। সে যে বিপ্লবীদলের, সে কথা সে গোপন করিয়া গেল।
দেওয়ান সাহেব ভ্রু-কুঞ্চিত করিয়া কী চিন্তা করিতে লাগিলেন। জিনিসপত্র গাড়িতে উঠাইয়া দিয়া দেওয়ান সাহেব বলিলেন, ‘আমি পুলিশ-কমিশনার সাহেবের কাছে যাচ্ছি। যেমন করে হোক ওর কিনারা করে তবে জলগ্রহণ করব।’
জাহাঙ্গীরের মাতা সাশ্রুনেত্রে দেওয়ান সাহেবের দিকে তাকাইয়া থাকিলেন। কিছু বলিতে পারিলেন না।
মাঝে মাঝে কেবল হারুণের উন্মাদিনী মাতা কাঁদিয়া উঠিতে লাগিলেন, ‘মিনা! মিনা কোথায় গেল আমার? সে আর ফিরবে না। আবার পালিয়ে গেল!’
এত আনন্দের মাঝে সহসা যেন ঝড় উঠিয়া সমস্ত লন্ডভন্ড হইয়া গেল।
জাহাঙ্গীরের মাতা কাঁদিলেন না। ঝড় উঠিবার পূর্বে প্রকৃতি যেমন শান্ত গম্ভীর মূর্তি ধারণ করে – তেমনি বিষাদ-ঘন মূর্তি লইয়া বাড়িতে আসিয়া উঠিলেন।
কাহারও মুখে কথাটি নাই। জাহাঙ্গীরের মাতা আদর করিয়া হারুণদের সকলকে বাড়িতে উঠাইয়া সকলের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। মুখরা মোমি এবং মোবারক পর্যন্ত কথাটি কহিতে সাহস পাইল না।
দ্বিপ্রহরে দেওয়ান সাহেব ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মুখ চোখ দেখিয়া জাহাঙ্গীরের মাতা ভয় খাইয়া গেলেন। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। কোনো রকমে দেয়াল ধরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, ‘দেওয়ান সাহেব! আমার খোকা?’
দেওয়ান শান্ত গম্ভীর স্বরে বলিলেন, ‘বিপ্লবীদের সাথে সে ধরা পড়েছে! হতভাগ্য!…’ তিনি আর বলিতে পারিলেন না। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল!
জাহাঙ্গীরের মাতা সকালে উঠিয়াই সমস্ত সংবাদপত্র আনাইয়া পড়িয়াছিলেন। এই দুই দিনের মধ্যে বাংলাদেশে যে ভীষণ ওলট-পালট হইয়া গিয়াছে – তাহাও তিনি জানিতে পারিয়াছেন সংবাদপত্র পড়িয়াই।
শত শত যুবক কারারুদ্ধ হইয়াছে। সেই ভীষণ জার্মান ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। সারা দেশ ব্যাপিয়া পুলিশ জাল ফেলিয়াছে! –
কাজেই দেওয়ান সাহেবের এই সংবাদ তিনি বজ্রাহতের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন। দাসী-বাঁদিরা যে যেখানে ছিল ছুটিয়া আসিল!…
কুহেলিকা – ২০ (শেষ)
বজ্রপাণি, প্রমত্ত প্রভৃতির সাথে জাহাঙ্গীরেরও দ্বীপান্তর হইল। তাহার সত্যকার নাম প্রকাশ পাইল না। জাহাঙ্গীর তাহার নাম বলিয়াছিল স্বদেশকুমার। সেই নামেই তাহার শাস্তি হইয়া গেল।
ফিরদৌস বেগম ও দেওয়ান সাহেব লক্ষাধিক টাকা খরচ করিয়াও তাহাকে বাঁচাইতে পারিলেন না।
যেদিন জাহাঙ্গীরের বিচার হইয়া গেল সেইদিন সন্ধ্যায় মাতা তাহার সহিত আলিপুর জেলে গিয়া দেখা করিলেন। মাতা আর সেখানে কাঁদিলেন না। শুধু বলিলেন ‘খোকা, তুই তো চললি, তোর এই ঐশ্বর্য কাকে দিয়ে যাব?’
জাহাঙ্গীর বলিল, ‘তুমিও কি চলে যাবে মা?’
মাতা শান্তস্বরে বলিলেন, ‘তুই তো আমায় থাকতে দিলিনে। আমি মক্কা গিয়ে একবার কাবা ঘরের ধুলায় লুটিয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করব খোদাকে – কেন তিনি এত বড়ো শাস্তি দিলেন?’
জাহাঙ্গীর বলিল, ‘আর তো তোমাকে নিষেধ করবার অধিকার আমার নাই মা। তুমি যেখানে গিয়ে শান্তি পাও, যাও। যদি ফিরে আসি, আর তুমি বেঁচে থাক, দেখা হবে!’… বলিয়াই একটু ভাবিয়া বলিল, ‘চম্পা এসেছিল তোমার কাছে?’
মাতা বলিলেন, ‘এসেছিল, কিন্তু আমি তাকে তাড়িয়ে দেয়েছি!’
জাহাঙ্গীর বলিল, ‘ভুল করেছ মা, ও ঐশ্বর্যের মালিক যদি আমিই হই, তাহলে ওই ঐশ্বর্যের ভার তারই হাতে ছেড়ে দিয়ো! আমার মার মতো শত শত মা আজ নিরন্ন, তাঁদের মুখে তাঁদের সন্তানের মুখে সে অন্ন দেবে। ও ঐশ্বর্য এখন আমার দেশের নির্যাতিত ভাই-বোনদের। এবার সে এলে তাকে ফিরিয়ো না। হাঁ, ভূণীকে আমার সম্পত্তির এক চতুর্থাংশ ছেড়ে দিয়ো। ও অনেক দুঃখ পেয়েছে।’
মা কিছুক্ষণ ভাবিয়া শান্তস্বরে বলিলেন, ‘আচ্ছা তাই হবে।’ তিনি অধর দংশন করিয়া কান্নার বেগ সামলাইতে লাগিলেন।
মাতার সহিত সকলেই আসিয়াছিল। জাহাঙ্গীর হাসিয়া হারুণের দিকে চাহিয়া বলিল, “তোমার কথাই সত্য হল কবি, নারী ‘কুহেলিকা’।” হারুণ কাঁদিয়া ফেলল।
ভূণী মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া কেবল একটা শব্দ নির্গত হইল, ‘নিষ্ঠুর’।
জেলের ভিতর পাগলা ঘন্টি বাজিয়া উঠিল। জেল ভাঙিয়া কয়েকজন রাজবন্দি পলাইয়াছে।
স-ওয়ার্ডার জেলার আসিয়া জাহাঙ্গীরকে লইয়া চলিয়া গেল।
মাতা সেইখানে পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, ‘খোকা! আমার খোকা!’
॥ সমাপ্ত ॥