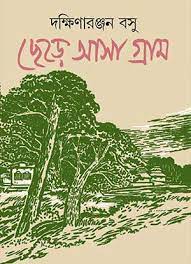অনেকের মনে একটা প্রশ্ন ছেড়ে আসা গ্রাম কি ধরনের সাহিত্য? ছেড়ে আসা গ্রাম – দক্ষিণারঞ্জন বসুর একটি জীবনী ও স্মৃতিচারণ সম্পর্কিত বই। ছেড়ে আসা গ্রাম বইটি পারুল প্রকাশনী ২০১৭ সালে প্রথম প্রকাশ করেন। আপনারা বইটি পড়তে চাইলে আর দেরি না করে এখনি শুরু করুণ এবং কোন প্রকার সমস্যা ছাড়াই বইটি পড়ে ফেলুন।
ছেড়ে আসা গ্রাম বইয়ের বিবরণঃ
- বইয়ের নামঃ ছেড়ে আসা গ্রাম
- লেখকের নামঃ দক্ষিণারঞ্জন বসু
- বিভাগসমূহঃ উপন্যাস
- প্রকাশনীঃ পারুল প্রকাশনী
- প্রকাশকালঃ ২০১৭
কুষ্টিয়া – শিলাইদহ ভেড়ামারা
প্রমত্তা নদী পদ্মা। জলকল্লোল প্রাণের জোয়ার, প্রাচুর্যের প্লাবন। সে প্লাবনে দু-তীরের গ্রামের মানুষদের অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। তাই গ্রামবাসীরা বড়ো দুঃখে প্রাণ-প্রবাহিনী পদ্মাকে নাম দিয়েছে কীর্তিনাশা। শুধু ধাও, শুধু ধাও, উদ্দাম উধাও। এই উদ্দামতার অত্যাচার সন্তানের আবদারের মতোই যেন সহ্য করে এসেছে আমার জননী, আমার প্রিয় জন্মভূমি শিলাইদহ। জনশ্রুতি আছে শেলি নামে একজন কুঠিয়াল সাহেবের নামানুসারেই গ্রামের নামকরণ হয়েছে শিলাইদহ। নদীর ধারে তাঁর কবরটি অনেকদিন পর্যন্ত গ্রামবাসীর কৌতূহল মিটিয়ে এসেছে। দুরন্ত পদ্মা এখন তা গ্রাস করে নিয়েছে। এমনি করে মানুষের কীর্তি নাশ করেছে পদ্মা এক দিকে, আবার অন্য দিকে নতুন কীর্তি গড়ে তোলার কাজে অকৃপণ সহায়তাও করেছে। কিন্তু আজ পদ্মাতীরের মানুষ পদ্মাকে ছেড়ে এসেছে যে দুঃখে, পদ্মা নিজেও ততখানি দুঃখ দেয়নি কখনো। এ দুঃখের মূল পদ্মা নয়, মানুষের জাতভাই মানুষ।
হাজার গ্রামের মধ্যে শিলাইদার এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল না যার জন্যে বাংলাদেশের মানুষ তাকে মনে রাখতে পারে। কিন্তু সে বৈশিষ্টতা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সোনারতরীর যুগে অনেক কবিতা রচনা করেছেন এই শিলাইদার কোল ছোঁয়া পদ্মার বোটে বসে বসে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িরই জমিদারির অন্তর্গত ছিল এই শিলাইদা।
গ্রামের মাটির স্পর্শ ভুলতে পারি না। ভুলতে পারি না দু-কূল-প্লাবিনী পদ্মকে। বেশ বুঝতে পারছি আজকের এই পরমাশ্চর্য সকালের রোদে নদীর ওপারে ঝাউগাছের দীর্ঘ সারির ফাঁক দিয়ে রোদের ঝলক সারাশিলাইদার গায়ে লুটিয়ে পড়ছে। নদীর ওপরে গাঙচিলগুলো মাছের লোভে চরকির মতো ঘুরপাক খাচ্ছে। আর জলের বুকে নৌকো বেয়ে চলেছে পদ্মানদীর মাঝিরা। কলকাতার এই মধুবংশীয় গলির প্রায়ান্ধকার কুঠুরিতে কোনোরকমে মাথা গুঁজে আজ অনুভব করছি শরতের প্রাক্কালে পদ্মা-স্নাতা শিলাইদার প্রকৃতি ও পরিবেশ। অকাল বর্ষণে নদী পদ্মার যৌবনমদিরতা হয়তো এখনও শেষ হয়নি। হয়তো জলতরঙ্গ এখনও তেমনই প্রবলতায় আছড়ে পড়ছে শিলাইদার দু-তীরে। সে কূলভাঙা ঢেউয়ের শব্দে কত রাত্রে ঘুম গেছে ভেঙে। কত ঝড়ের রাতে পদ্মানদীর মাঝিদের হাঁকাহাঁকিতে সচকিত হয়ে উঠত আমার কিশোরমন। ভাবতাম এই দুরন্ত, দুর্বার পদ্মার বুকে ভগবান যে-মানুষদের জীবন-সংগ্রামে ঠেলে দিয়েছেন তারা যেন প্রকৃতির পরিহাসকে অনায়াসে ভ্রুকুটি দেখিয়ে এই দুর্দম ঝড়ের মধ্যেও নদী পারাপার করছে। এ শক্তি মানুষ অর্জন করেছে নিজেদের বাঁচবার অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে। কিন্তু সেই মানুষেরাই আবার আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ভুলে গিয়ে আত্মধ্বংসী সংগ্রামে কী করে মেতে ওঠে?
পুজো এগিয়ে আসছে। প্রতিবছরই এ সময়টাতে শিলাইদা যাওয়ার জন্যে মন উন্মুখ হয়ে উঠত। কুষ্টিয়া স্টেশনে নামলেই মন এক অপরিসীম আনন্দে ভরে যেত। সামনে গড়াই। নৌকো দিয়ে গড়াই নদী পার হয়ে গিয়ে পৌঁছোতাম কয়াতে। আর দূর নয়। আর মাত্র তিন মাইল হাঁটাপথ। দু-পাশে অতিপরিচিত আমবন, বাঁশঝাড় আরও কত বনলতার শ্যামল স্নিগ্ধ
স্পর্শ। ভাঙা রাস্তা। তার ওপর দিয়ে আবার রহিম ভায়ের গোরুর গাড়ির অত্যাচার। তবুও কলকাতার পিচঢালা রাস্তার চেয়ে সে পথকেই আপন বলে জেনেছি, সে-পথ যে আমার গ্রামের ভিটার সন্ধান দিত আমাকে। বর্ষাকালে জল, শীতকালে ধুলো। তবু যেন কী এক প্রশান্তি সারামন জুড়ে থাকত সে পথে চলবার সময়, তা আজ বোঝাই কী করে? পথ-চলতি মানুষদের সুবিধের জন্যে ঠাকুরবাড়ির লোকেরা পথের দু-পাশে অনেক বাবলা গাছ লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কয়া থেকে কুঠিবাড়ি, কুঠিবাড়ি থেকে শিলাইদহ কাছারি পর্যন্ত এই বাবলা গাছের সারি। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত সে বাবলা শ্রেণিকে কোনোদিনই তো ভুলতে পারব na। গাছগুলোকে দেখলেই মনে হত যেন আপনার ছত্রছায়ায় আশ্রয় দেওয়ার জন্যে দূরদেশের প্রবাসী সন্তানদের পথ চেয়ে ব্যাকুল আগ্রহে তারা অপেক্ষারত। শুধু গাছ নয়, পথিকদের সুবিধের জন্যে ঠাকুরপরিবারের কর্তারা রাস্তার পাশে একটি বড়ো পুকুর ও টিউবওয়েল খনন করিয়ে দিয়েছেন। বাড়ি যাওয়ার পথেই কত কুশল প্রশ্ন। কেউ বলে : ‘বাবু কখন আসতিছেন?’ কিছুদূর যেতেই আবার প্রশ্ন : ‘আপনি বাড়ি আসেন না কো? আপনের মা আমার কাছে কত প্যাচাল পাড়েন! বাড়ি গিয়ে হয়তো শুনি ওইলোক অনেকদিন আসেইনি আমাদের বাড়ি। তবু সহজ আন্তরিকতায় কুশল প্রশ্ন করতে কার্পণ্য করে না কেউ। হয়তো বলি : ‘তা তোমাদের দেখবার জন্যেই তো এতদূর থেকে এলাম।’
‘তা কয়েকদিন আছেন তো? কাইল আমার খাজুর গাছ নাগাইছি। আপনার জন্যে এক হাড়ি রস দিবার মন করি।’–কোথা থেকে ছুটে এসে জিজ্ঞেস করে জব্বর। কাছারির গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান জব্বর মুনশি। ওর বাড়ির সামনে দিয়ে যেতে দেখলেই জোর করে নিয়ে যাবে বাড়িতে। কিছু না খাইয়ে কিছুতেই আসতে দেবে না। এমন মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল সবার সঙ্গে।
বাড়ি থেকে আধ মাইল দূরে। খোরশেদপুর এম. ই. স্কুল। এই স্কুলেই বিদ্যা শিক্ষার হাতেখড়ি আমার। খোরশেদপুরের স্কুলজীবনে মাত্র তিনদিন স্কুল পালিয়েছিলাম। বড়ো রাস্তা ছাড়া একটা জঙ্গলের পথেও স্কুলে যাওয়া যেত। এই জঙ্গল সম্পর্কে নানারকম জনশ্রুতি রয়েছে। ভূতের জঙ্গল বলে ছিল এর পরিচয়। বলা বাহুল্য কোনোদিন ভূত কিংবা ভূতের বাসস্থানের আমরা সাক্ষাৎ পাইনি। স্কুল পালিয়ে খেত থেকে মটরশুটি চুরি করে এনে বনের ভেতর গাছতলায় বসে বসে খেতাম। একদিন ধরা পড়ে যাওয়ার পর আর স্কুল পালাইনি। মাঝে মাঝে আবার শিকারে বের হতাম। কোনোদিন নদীর ধারে খরগোশ শিকারের আশায়, কোনোদিন দক্ষিণ দিকের জঙ্গলে বাঘের বাচ্চা ধরবার উদ্দেশ্যে মহড়ায় বের হতাম। কিন্তু কোনোদিন একটা ফড়িংও ধরতে পারিনি। এমনই সব অদ্ভুত খেয়ালে পাঠ্যজীবনটা কাটিয়েছি বেশ। একবার দেবুর আর আমার মাথায় খেয়াল চাপল যে ডাকাতি করে গরিবদের দান করতে হবে। যে কথা সেই কাজ। খেলার ছোটো পিস্তলটি নিয়ে রাত দশটার সময় বাইরের ঘর থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে পড়লাম আমি আর লেফটেন্যান্ট দেব। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারিনি। পাশের বাড়িতেই প্রথম মহড়া দিতে গিয়ে কী যে নাকাল হয়েছিলাম সে করুণ কাহিনি প্রকাশ না করাই ভালো। অবশ্যি এমন সব বুদ্ধি হত ডিটেকটিভ বইয়ের নানা আজগুবি গল্প পড়ে।
কিশোরজীবনের এই রূপকথার রাজ্যে মূর্তিমান বাস্তব ছিলেন গফুর মাস্টার। আমার জন্মের পূর্ব থেকেই গফুর মাস্টার আমাদের গৃহশিক্ষক। দাদা-দিদিদের হাতেখড়ি দিয়েছেন তিনিই। কলকাতায় এসে অনেক কৃতবিদ্য শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষালাভ করে ধন্য হয়েছি, কিন্তু কোনোদিন গফুর মাস্টারকে ভুলতে পারিনি। কলকাতার পথে চলতে চলতে রেডিয়োতে একটা গান শুনলাম : নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহি রে। ওগো আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে। গানটা শুনে আমার মন চলে গেল অনেক দূরের স্মৃতির রাজ্যে শিলাইদার এক প্রান্তে, কোন এক মুগ্ধ কিশোরমনের চিত্র সেটি। ঢল নেমেছে পদ্মার দু-তীরে। সারাটা আকাশে কে যেন কালি ঢেলে দিয়েছে। পুবদিকের জানলাটা খোলা। মনে পড়ল রবীন্দ্রনাথ এমন দিনেই হয়তো এখানকার পদ্মার বোটে ‘সোনার তরী’ আর ‘খেয়া’র কবিতাগুলি রচনা করেছিলেন। সেদিনও আকাশ হয়তো এমন মেঘাবৃত ছিল। সেই মেঘমেদুর অম্বরের প্রান্তঘেঁষা তাল-তমাল বন লক্ষ করে একদিন, সে বহুদিন আগে, আরও একজন কবি ‘শতক যুগের গীতিকা’য় সুর সংযোজন করেছিলেন। মন তখন অতীতমুখর। শুনতে পেলাম পদ্মানদীর মাঝি সুর ধরেছে : ‘কুল নাই, কিনারা নাই, নাইকো গাঙের পাড়ি, সাবধানেতে চালাইও মাঝি আমার ভাঙা তরি। সে দিন আর বুঝি ফিরে আসবে না!
রবিবার আর বুধবার এই দু-দিন বাজার বসত গ্রামে। বাকি পাঁচদিন গোপীনাথ দেবের মন্দিরের সামনে বসত বাজার। বাজারের পাশ দিয়েই পদ্মা প্রবাহিতা। চৈত্র-বৈশাখ মাসের পদ্মা আর বর্ষাকালের পদ্মা যেন আকাশপাতাল তফাত। পদ্মার এই দুটো রূপকেই আমি ভালোবাসি। দারুণ গ্রীষ্মের দাবদাহে পদ্মা নিস্তেজ হয়ে পড়ে। আবার বর্ষার কালোমেঘ দেখলেই পদ্মা যেন উন্মাদের ন্যায় উত্তাল তরঙ্গ ভেঙে দুর্বার হয়ে ওঠে।
এই আমার শিলাইদা। আজ তার পরিচয় দিতে গিয়ে কেবলই মনে হচ্ছে শিলাইদহে জন্মগ্রহণ করে আমি ধন্য হয়েছি। রবীন্দ্রনাথ এই শিলাইদহকে খুব ভালোবাসতেন। এখানকার কুঠিবাড়িটি ছিল তাঁর নিজস্ব। এখানে থাকতেই তিনি ‘গীতাঞ্জলি’র ইংরেজি অনুবাদে হাত দেন। এখান থেকে কিছু দূরেই স্বৰ্গত সাহিত্যসেবী জলধর সেনের বাড়ি কুমারখালি। সব স্মৃতির বন্ধনই অটুট আছে, কেবল দেশের ব্যবধান গেছে বেড়ে। তবুও আমি শিলাইদহকে ভুলতে পারি না। মনে হয় আবার আমার গ্রামকে ফিরে পাব, ফিরে পাব গফুর মাস্টার, জব্বর মুনশি, সবাইকে।
.
ভেড়ামারা
পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে।
পিছিয়ে পড়েছি আমি, যাব যে কী করে।।
এসেছে নিবিড় নিশি, পথরেখা গেছে মিশি;
সাড়া দাও, সাড়া দাও আঁধারের ঘোরে।।
কবিগুরুর গানটি আজ আমাদের মনের কথা ব্যক্ত করছে। পথের ডাককে অগ্রাহ্য করতে না পেরে আজ আমরা মৃত্যুর পথে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছি অন্ধকার নিশিতে। অপটু-চরম ক্লান্তিতে পড়েছে ভেঙে, পথরেখা মুছে গেছে সম্মুখ থেকে, ফলে জীবনযাত্রায় আমরা পড়েছি পিছিয়ে–এ সময় এমন একটি ধ্রুবতারারও সন্ধান পাচ্ছি না যার আলোর নির্দেশে আমরা এগিয়ে গিয়ে নির্বিঘ্নে জীবনে হব সুপ্রতিষ্ঠিত। আমরা মায়ের কোল থেকে ছিটকে পড়েছি দূরে। শস্যশ্যামলা গ্রাম্য পরিবেশ ছেড়ে রুক্ষ শহুরে আবহাওয়ায় যেন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। ললাটে জন্মভূমির কোমল স্পর্শের জয়তিলক নিয়ে জন্মের প্রথম শুভক্ষণে কান্নার সুরে ‘মা-মা’ বলে আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলাম একদিন আজ জীবন-মধ্যাহ্নে কাঁদতে কাঁদতে আবার আশ্রয় প্রার্থনা করছি দেশজননীর কাছে। সেদিন পেয়েছিলাম গ্রাম-জননীর কোল, আজ তাঁর কাছ থেকে বিতাড়িত। সেদিন আর এদিনের মধ্যে পার্থক্য অনেক, আজ আমার চলার পথে কাঁটা, শ্বাস প্রশ্বাসে নাগিনির সুতীক্ষ বিষ! দ্বীপান্তরিত লাঞ্ছিত জীবন নিয়ে সর্বদাই বিব্রত। কেবল নিজের চিন্তায় সব সময় বিভোর। তবু মন পড়ে আছে সেই সুদূরে হারানো মায়ের কোলে, পল্লির ছোট্ট কুটিরে, আমার গাঁয়ের শ্যামঘন-নীলাকাশে। সেসব দিনকে আজ দিকচক্রবালে স্বপ্নের মতো মনে হয়। জানি না দেশজননী আবার মা-জননীর মতো কোলে ঠাঁই দেবেন কি না, আবার আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ পাব কি না!
জীবনের ওপর বিতৃষ্ণা এলেই চোখের সামনে ছবির মতো ভেসে ওঠে আমার গ্রামখানি। আমার গ্রাম ভেড়ামারা আমার কাছে অতুলনীয়, বার-বার গ্রামের নাম উচ্চারণে শান্তি পাই মনে। মনের কোনো গোপন কোণে সেই ‘ভেড়ামারা” নামটি বোধহয় খোদাই হয়ে আছে, না হলে আজ এই দুঃসময়ের মধ্যেও তাকে এত নিবিড়ভাবে মনে পড়ে কেন? কেন তাহলে এই অখ্যাত অজ্ঞাত গ্রামটির তুলনা খুঁজে পাই না? কেন সেই শান্তির নীড় স্নিগ্ধ সমীর’-এর কথা চিন্তা করলে চোখ জলে ভরে আসে? আজ ভেবে আশ্চর্য লাগে আমার গ্রাম আমার কাছে কেন বিদেশ হয়ে গেল একরাত্রির মধ্যে? প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা গ্রামখানি কেন হঠাৎ লক্ষ্মীছাড়া হয়ে গেল?
আমার গ্রাম পূর্বে ছিল নদিয়া জেলায়, আজ হয়েছে কুষ্টিয়া জেলার কুক্ষিগত। আগে এই কুষ্টিয়াও ছিল নদিয়া জেলারই একটি মহকুমা। এককালে একটি ব্যাবসা-বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল আমার গ্রাম। কলকাতার পণ্যের বাজারে তাই ভেড়ামারার একটি নির্দিষ্ট স্থান ছিল বাঁধা। একদিন এখান থেকেই পাট আর পান রপ্তানি হত ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে রেল ওয়াগন ভরতি হয়ে। ইলিশ মাছও বাদ যেত না সে তালিকা থেকে। মাইল তিন চার উত্তরে পদ্মা নদীর ধারে ‘রাইটা’ থেকে বরফ দিয়ে মাছের সেরা ইলিশ মাছ আসত ভেড়ামারা স্টেশনে বিভিন্ন স্থানে রপ্তানি হওয়ার জন্যে। বৃদ্ধদের মুখে শুনেছি একদা এখানে নাকি বাইশ তেইশটি ইলিশ মাছ মিলত একটাকায়। কুটুম্ববাড়ি যেতে হলে তাঁরা একটাকার ইলিশ মাছ কিনে নিয়ে যেতেন মুটের মাথায় চাপিয়ে! সেই মাছ অবশ্যি শুধু কুটুম্বরাই খেতেন না, আশপাশের আরও অনেকেই রসাস্বাদন করতেন তার। আমরা অতটা না দেখলেও তার খানিকটা আভাস পেয়েছি। খাদ্যদ্রব্য খুব সস্তাই ছিল এখানে, আজ আর অবশ্যি সেদিন নেই। এখন সব কিছুই অগ্নিমূল্য। এখন মাছ থাকলে তেল থাকে না, তেল থাকলে মাছের অভাব ঘটে। সেদিনের রাম যখন নেই, তখন অযোধ্যার অন্বেষণ করা বৃথা। কেন হল এই দৈন্য? গরিব মানুষের কি সুবিধে হয়েছে দেশ-দ্বিখন্ডিত হয়ে? দেশমাতার অঙ্গচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষেরও যে অঙ্গচ্ছেদ হয়েছে সে-কথা মোটেই আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। আগেকার কথা ভেবে তাই অস্থির হয়ে পড়ি সময় সময়, কিন্তু আমার অস্থিরতার মূল্যই বা কী? চেষ্টা করলে পারি না কি আবার আমরা এক হতে? পারি না কি দেশের বুকের ওপর যে শ্বাসরোধক প্রাচীরটা তোলা হয়েছে তাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিতে পারি নাকি আবার আমরা পরস্পরকে বিশ্বাসভরে আলিঙ্গন করতে? কাকে ছেড়ে কার চলবে? তবে কেন সমস্ত মানবিকতাকে বিসর্জন দিয়ে আমরা সাম্প্রদায়িক দৈত্যের দাসত্ব করব জীবনভোর?
গ্রামে বাস করার কোনো অসুবিধেই ছিল না। সরকারি হাসপাতাল, হাই স্কুল, থানা, স্টেশন, নদী ইত্যাদি কোনো কিছুরই অভাব ছিল না। আশ্বিন-কার্তিক মাসে গ্রামখানিতে যেন লক্ষ্মীশ্ৰী ফুটে উঠত। সব দিকে ব্যস্ততা। সে সময় এত পাট আমদানি হত যে পাটের কাঁচা গন্ধে বাতাস হয়ে উঠত ভারী। একমাত্র পাটকে কেন্দ্র করেই লক্ষ লক্ষ টাকার আদান-প্রদান চলত প্রতিদিন। কলে পাট চাপানো হত–সেই সময়ে কুলিদের সমস্বরে গাওয়া খুশিভরা বিচিত্র ‘হো-আই-লো’ গানের সব টুকরো টুকরো কলি আজও সময় সময় কানে এসে বাজে যেন। অন্য সময় চাল-ধান, ছোলা-মটর আর পানের ফলাও কারবারে ব্যাবসায়ীরা থাকতেন ব্যতিব্যস্ত। লক্ষ্মীর ধ্যানে সকলেই থাকতেন মশগুল, অন্য দিকে মন দেওয়ার তেমন অবসরই থাকত না কারও। দুঃখ হয় সেদিনের কথা ভেবে, কোথায় গেল সেই মধুর দিনগুলো।
মনে পড়ে পুণ্যাহে’র সময় জমিদারের কাছারিতে সে কী খাওয়া-দাওয়ার ঘটা! আকণ্ঠ চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয়ের পর বাড়ি ফিরতাম শোলার একটা মালা গলায় দিয়ে। এই ‘পুণ্যের আসরে কোনোদিন জাতিভেদ দেখিনি। হিন্দু প্রজা মুসলমান প্রজা সমান উৎসাহের সঙ্গেই জমিদার বাড়িতে খেয়ে এসেছে, গল্পগুজবে মশগুল হয়ে একই সঙ্গে ফিরে এসেছে আপন আপন বাড়িতে। জানি না হঠাৎ সেই মধুর সম্পর্কের মধ্যে কী করে ফাটল ধরল, ‘পুণ্যের মধুর বন্ধনে পাপের প্রবেশ ঘটল কখন কী করে!
আমাদের বাড়ির সামনেই বসত হাট। সপ্তাহে দু-দিন। মনিহারি, জামা-কাপড় থেকে শুরু করে মাটির হাঁড়ি, কলসি, মশলা, প্রায় সব কিছুই পাওয়া যেত হাটে। তরিতরকারি এবং মাছ-মাংস তো বটেই। গ্রামের হাটের সঙ্গে কোথায় যেন একটা বিরাট পার্থক্য আছে শহুরে বাজারের। হাটের সঙ্গে গ্রামের অতিসাধারণ মানুষেরও একটা সুনিবিড় সম্পর্ক আছে। তেমন সম্পর্কের কোনো হদিশ মেলে না শহুরে বাজারে। আমাদের গ্রাম্য হাটটি তাই ছিল একাধারে মিলনক্ষেত্র এবং শিক্ষাক্ষেত্র। সপ্তাহে দু-দিন কেনাকাটা করতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে দূরগ্রামের লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎও হয়ে যেত হাটে। আমরা জিনিস কেনার জন্যে যত না হাটে। গেছি তার চেয়ে বেশি গেছি বন্ধুজন ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে চাক্ষুষ আলাপের জন্যে। এই যে আমাদের গ্রামকেন্দ্রিক আত্মীয়তাপূর্ণ মন তা বিনষ্ট হল কেন? সেই সুন্দর পল্লিজীবন, সেই গোচারণ ক্ষেত্র, সেই মর্মরধ্বনি মুখরিত বেণুকুঞ্জ কোন পাপে আমাদের জীবন থেকে নির্বাসিত হল কে জানে! পল্লিজীবনের সুস্নিগ্ধতা, সরলতা আর বনপ্রান্তরের সৌন্দর্য ও পাখির কাকলি দিয়ে যে জীবন ছিল ঘেরা সে জীবন কি আবার ফিরে পেতে পারি না? পল্লিগ্রামগুলো বাঙালির জাতীয়জীবনের মূল আশা এবং আশ্রয়স্থল। সেই পল্লি থেকেই আমরা হলাম বিচ্যুত! কিন্তু আমাদের কী দোষ?
আজ বেশি করে মনে পড়ছে ‘মায়ের বাড়ি’র কথা। গ্রামবাসীর প্রাণকেন্দ্র হিসেবেই ধরা হত ‘মায়ের বাড়ি’কে। এখনও পর্যন্ত সেই মায়ের কথা চিন্তায় এলেই আপনা আপনি কপালে হাত দুটি উঠে প্রণামের মুদ্রায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। বিনা প্রণামে মায়ের কথা বলা ভেড়ামারার লোকেরা চিন্তাই করতে পারে না। দুর্গাপুজো হত এখানে অত্যন্ত ধুমধামের সঙ্গে। মানতের চিনি সন্দেশের যে হাঁড়ি পড়ত তার সংখ্যানির্ণয়ে ফুরিয়ে যেত ধারাপাতে শেখা যত সংখ্যাসমষ্টি! এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত শ্রেণিবদ্ধ হাঁড়ির সারি দেখে শৈশবে বিস্ময়াবিষ্ট হতাম। সারাবছরের মানত শোধ করা হত এই পুজোর সময়। পাছে গোলমাল হয়ে যায় এই ভয়ে প্রতিটি হাঁড়ির গায়ে খড়ি দিয়ে স্পষ্টাক্ষরে নাম লেখা থাকত গৃহস্বামীদের। ছোটো গ্রামখানির বুকে পুজোর কটাদিন ধরে চলত জীবনের জোয়ার। দূর-দূরান্তরের নর-নারীরা আসত মেলা দেখতে, বিগ্রহ দর্শন করতে, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে। একই সঙ্গে পুজো দেখা, আত্মীয়দর্শন এবং জিনিসপত্র কেনাকাটার সুযোগ পল্লিগ্রামে বড়ো বেশি আসে, তাই-দর্শনার্থীর প্রাচুর্য চোখে লাগার মতোই হত। আজও সেইদিনকার ছবি স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠেছে চোখের সামনে। কী সুন্দর গ্রামবাসীদের হাসিখুশি মাখানো মুখগুলো, তাদের ত্বরিত চরণ ধ্বনি, বিশ্রাম ও ব্যস্ততায় হিল্লোলিত অপূর্ব জীবনছন্দ। মনে হচ্ছে যেন দেখতে পাচ্ছি মা দুর্গার সামনে করজোড়ে অঞ্জলি দেওয়ার দৃশ্য–শুনতে পাচ্ছি বৃদ্ধ পুরোহিতের উদাত্ত কণ্ঠের মন্ত্রপাঠ,
অন্ধ্যং কুষ্ঠংচ দারিদ্রং রোগং শোকংচ দারুণম।
বন্ধুস্বজনবৈরাগ্যং হরমে হরপার্বতি।
দুর্গাপুজো সমগ্র বাংলারই পুজো। সেখানে, জাতিভেদের কথা ওঠে না। পুজোর সময় সারাগ্রামে একটা জাতিই চোখে পড়ত তা হল মনুষ্যজাতি। সেইজন্যেই অঞ্জলির পর প্রসাদ গ্রহণের ব্যস্ততা দেখেছি শুধু হিন্দুদের মধ্যে নয়, মুসলমান ভাইদের মধ্যেও। অস্থিমজ্জায় এই যে একাত্মবোধ সেদিন ছিল তা কোথায় গেল আজ? সেদিন তো দেখেছি হরপার্বতী বা উমাকে নিয়ে যে গান হত তাতে উমার দুঃখে কত মুসলমান ভাই-বোনও অশ্রুবিসর্জন করেছেন।
ভুলতে পারছি না ঝুলনের সময় ঠাকুরবাড়ির যাত্রাগানের কথা। সেদিনটি যেন ছিল সমস্ত গ্রামবাসীর জীবনের একটি পরমলগ্ন। সারাবছরের প্রতীক্ষার পর আসত ওই দিনটি। আমার বয়েস ছিল অল্প, তাই উৎসাহও ছিল অনন্ত। সন্ধে না হতেই খেয়েদেয়ে ঠিকঠাক হয়ে যাত্রার আসরে চলে যেতাম। জায়গা না পাওয়ার ভয়ে অভিনয়ের বহুপূর্বেই জায়গা সংগ্রহ করে উদগ্র প্রতীক্ষায় বসে থাকতাম সমস্ত ঠাট্টা-বিদ্রূপ অগ্রাহ্য করেই! ভিড় হত অসম্ভবরকম। ঠাকুরবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মাড়োয়ারিরা। গ্রামের লোক ঠাকুরবাড়িকে খুব শ্রদ্ধা করত। বাড়ির সামনে কালীঘরে কালীপুজো উপলক্ষ্যে গান বাজনার আসর বসত হামেশাই। কালীপুজোর দিন বাড়ির গুরুজনেরা আমাদের টিকিটি দেখতে পেতেন না, আমরা সবাই থাকতাম মহাব্যস্ত। বলির পাঁঠাদের তত্ত্বতল্লাশ করতাম, মহাযত্নে তাদের কাঁঠালপাতা খাওয়াতাম, তাদের কোলে করে আদর করতাম সমস্ত দিন! কিন্তু এত আদরযত্নে যাদের লালন করলাম সমস্তটা দিন ধরে সেই স্নেহের জীবটিকে মুহূর্তে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে কোনো ব্যথাই অনুভব করিনি! মনের এই দ্বৈতপরস্পর-বিরোধিতার গুণগত ব্যাখ্যা করার বয়েস তখন না হলেও আজ খুব বিস্ময় লাগে তা ভাবতে। সেই জিনিসই কি গোটা বাংলার বুকে ঘটে গেল না?
‘নরমেধযজ্ঞ’ বা ‘নহুস উদ্ধার’ অভিনয় আমাদের একদিন সকলকেই মোহাবিষ্ট করত আজও বেশ মনে পড়ে। অভিনয়ে সুদখোর রতন দত্তের চাপে পড়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ সিদ্ধার্থ তার শিশুপুত্র কুশধ্বজকে তুলে দিলেন রাজা যযাতির নরমেধযজ্ঞে বলি দেওয়ার জন্যে। এই দৃশ্য দেখে আমরা সেদিন জাতিধর্ম-নির্বিশেষে ডুকরে কেঁদে উঠেছি। লক্ষ করেছি আসরের আবহাওয়া মুহূর্তে পালটে গেছে শোকের গভীরতায়, কোনো দর্শকের চোখ সেদিন শুকনো ছিল না। অভিনয় সার্থক হয়ে যেন বাস্তবের রূপ পেত। আজ নহুসের কথাই বেশি করে মনে পড়ছে এইজন্যে যে তার প্রেতাত্মা কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছে শুনতে পাচ্ছি। তার উদ্ধারের জন্যে মানুষের রক্ত চাই,–সে রক্তক্ষরণ তো হল এই বিশ শতকের শেষার্ধে! এখনও কি আমার উদ্ধার আশা করা যায় না নহুসের সঙ্গে সঙ্গে? এত রক্ত কি বিফলে যাবে? আমার মনে হয়, এই যে বিচ্ছেদ আজ এসেছে তা মিলনেরই ভূমিকামাত্র। সীতা’ অভিনয়ে আমরাই তো জোরগলায় শ্রোতাদের শুনিয়েছি,
জননি আমার
হেন প্রশ্ন তুমি কর দেবী?
বাল্মীকির রাম-সীতা চির-অবিচ্ছেদ;
অন্তরে অন্তরে চিরন্তন
মিলনের প্রবাহ বহিছে।
মনে হয় এই মিলন-প্রবাহ অধুনা ক্ষীণ হলেও একদা প্রাণগঙ্গায় জোয়ার এসে সমস্ত ক্লেদ নিয়ে যাবে ভাসিয়ে। বাল্মীকি মহাকবি, তাঁর কথা মিথ্যে হতে পারে না। আমরা সে মিলনের জন্যে আগ্রহে প্রতীক্ষা করব। ‘আসিবে সে দিন আসিবে।’
হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি, মাড়োয়ারি বলে আমাদের গ্রামে কোনো পার্থক্য দেখিনি। বহু মাড়োয়ারি এসে বাস করতেন ভেড়ামারায়, কিন্তু লক্ষ করেছি সবাই থাকতেন মিলেমিশে এক হয়ে। দেখেছি দু-পাঁচশো টাকা দরকার হলে চেয়ে আনত একজন অন্য আর একজনের কাছ থেকে। লেখাপড়ার কোনো দরকার হত না তার জন্যে। এই যে আত্মবিশ্বাস এর ওপরেই ছিল সেদিনকার প্রাত্যহিক জীবন। পরিশোধের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। এই লেনদেনে কোনোদিন কোনো কলহবিবাদ দেখিনি আজকের মতো। এত সুবিধে-সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেউ কাউকে বড়ো একটা ঠকায়নি বা অবিশ্বাসের কোনো কাজ করেনি। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করত, পরামর্শ দিত, পরামর্শ শুনত, পরামর্শমতো কাজও করত দ্বিধাহীনচিত্তে। সেখানে হিন্দু-মুসলমান বা মাড়োয়ারির গন্ডি টেনে জনজীবনকে কেউই সীমাবদ্ধ করত না। মাড়োয়ারি বন্ধুদের বাড়িতে প্রায়ই জুটত নিমন্ত্রণ। খাওয়াতে তাঁরা ছিলেন মুক্তপ্রাণ। বাড়িতে বেড়াতে গেলেও খাওয়ার ঘটা দেখে চোখ উঠত কপালে! তাঁদের ‘লাড়ু-মন্ডা-টিকরা’র স্বাদ এখনও ভুলতে পারিনি। সেই ঘিয়ে জবজবে খাবার এখনও জিভকে সরস করে তোলে সময় সময়! কোথায় সেদিন? কোথায় সেই মনের আত্মীয়তা? কোথায় সেই ভেড়ামারা?
অনেক সময় বাবাকে গ্রামের বাইরে যেতে হত দীর্ঘদিনের জন্যে। আমরা তখন ছোটো। মা থাকতেন একা অতবড়ড়া বাড়িতে আমাদের ক-জন নাবালককে নিয়ে। ক্ষুদিরামদাদা কিংবা ভবতারণ জ্যাঠার বাড়ি একটু দূরে ছিল বলে সব সময় খোঁজখবর নিতে পারতেন না তবু আমরা অসহায় বোধ করিনি কোনোদিন। সামনের রিয়াজুদ্দিন মন্ডল আর পাশের গৌরীশংকর আগরওয়ালা সর্বদাই খোঁজ নিতেন। আমাদের কোনোকিছুর প্রয়োজন হলে সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবস্থা করতেন। বাড়িতে পাহারা দিত জমিজমা তদারককারী আলিমুদ্দিন কিংবা কলিমুদ্দিন। তাদের আমি ‘দাদা’ বলে ডাকতাম। কোনোদিন তাই মনে হয়নি তারা মুসলমান বলে দূরের কেউ। তারা আমার অগ্রজতুল্য, যেখানেই থাকুক তারা সুখে থাকুক এই কামনাই করছি।
মনে পড়ছে এই আলিমুদ্দিনদা আর কলিমুদ্দিনদাই আমাদের প্রথম এসে বাধা দিয়ে ছলছল চোখে বলেছিল, ‘জমি-জায়গা বিক্রি করবেন না, বাবু! দেশ ছেড়ে কোথায় যাবেন? কতদিন থেকে আপনাদের খেয়ে আপনাদেরই কাছে পড়ে রয়েছি। এত সহজেই মায়া কাটিয়ে চলে যেতে পারবেন?’ কই তারা তো সম্প্রদায়ের গন্ডি টেনে আমাদের দূরে সরাতে চায়নি, রাজনীতির যূপকাষ্ঠে দেশকে দ্বিখন্ডিত করতে চায়নি, দেশের এবং জনগণের অভিশাপে অভিশপ্ত হয়ে উৎসাহ দেখায়নি। তারা গ্রামের নির্বিরোধ নিরীহ প্রজা, তাদের সামনে লোভের মোহ নেই। তাই তারা কেঁদেছিল আমাদের চলে আসার সময়।
যাবার বেলা সকলেই পিছু ডেকেছে, বাধা দিয়েছে পিতৃভিটে বিক্রির বিরুদ্ধে। আত্মীয়-অনাত্মীয়েরা কেঁদেছে, মাড়োয়ারিদের মা-বউরাও স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেছে। গাড়ির জানলা দিয়ে দেখেছি আমার অতিপ্রিয়জনরা প্ল্যাটফর্মে করুণ মুখে, সিক্ত নয়নে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকের চোখেই ফিরে আসার মিনতি। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেছে–তোমরা তো চলে গেলে, আমরা কী করব? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি। কাপুরুষের মতো মুখ লুকিয়ে এড়িয়ে গেছি সে-কথা। আজ ধিক্কার দিই নিজেকে,–জানি না যারা সেদিন এ প্রশ্ন তুলেছিল তারা আর কোথাও সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছে কি না। জানি না আজ তারা কোন ক্যাম্পে মাথা গুঁজে মৃত্যুকে এড়িয়ে চলেছে? আমাদের বাড়ির বুড়ি ঝি এখনও কি বেঁচে আছে?
এখনও চোখ বন্ধ করলে, কান ঢাকলে শুনতে পাই রেলগাড়ি চলার শব্দ। সেদিন যে ট্রেন ভেড়ামার থেকে বাঁশি বাজিয়ে ছেড়েছে আজও যেন তার গতিরোধ হয়নি। জানি না নিরবধি কালের কোন পর্যায়ে সে আমাদের নির্বিঘ্নে স্টেশনে পৌঁছে দেবে,–সেই গতিহীন অনন্তযাত্রার সমাপ্তির রেখা কবে দেবে টেনে।
স্বপ্নে হঠাৎ হঠাৎ প্রায়ই যেন কানে আসে–’কোথায় যাবেন বাবু, এত সহজেই কি গাঁয়ের মায়া কাটিয়ে চলে যেতে পারবেন?’–চমকে উঠে বলি–আলিমুদ্দি-কলিমুদ্দি দাদা! তোমাদের কথাই ঠিক, তোমাদের মায়া কাটানো সোজা নয়, তোমরা আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাও। আমাদের কথা কি আলিমুদ্দিনদাদাদের কানে কেউ পৌঁছে দেবে? আবার কি আমরা ফিরে পাব পল্লিজীবনের সেই মধুর পরিবেশ?
খুলনা – সেনহাটী শ্রীপুর ডাকাতিয়া
নদীর নাম ভৈরব। নদী নয়, নদ। কিন্তু ভৈরবের সে-রুদ্র প্রকৃতি এখন আর নেই। কয়েক বছর আগে খুলনা জেলার গ্রামান্তে এই নদ একবার তার রুদ্ররূপ ধারণ করেছিল। দু-তীরের জনবসতি কুক্ষিগত করে নিয়েছিল সে উদ্দাম উত্তাল ভৈরব। তারপর আর নয়। মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো সে পড়ে আছে পদপ্রান্তে, আমার গ্রাম সেনহাটীর পদপ্রান্তে। পূর্ববাংলার অন্যতম বিখ্যাত গ্রাম এই সেনহাটী। অনেক ইতিহাস বিজড়িত হয়ে আছে এর সঙ্গে। জনশ্রুতি আছে, বল্লাল সেন তার জামাতা হরি সেনকে ‘জামাইভাতিস্বরূপ এই গ্রামখানি দান করেছিলেন। হরি সেনই তার নাম রাখেন ‘সেনহাটী’। কবিরামের দিগ্বিজয়-প্রকাশ গ্রন্থে বলা হয়েছে লক্ষ্মণ সেন সুন্দরবনের জঙ্গল কেটে যশোহরের কাছে ‘সেনহাটী’ নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সে যাই হোক, ইতিহাসে আজ আর প্রয়োজন নেই। সেনহাটী আজ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।
সে গ্রামেরই ছেলে আমি। সেজন্যে আমি গৌরবান্বিত। গ্রামের দক্ষিণ দিকে ভৈরব নদ। এ গ্রামে প্রবেশের প্রধান পথ দক্ষিণ দিকেই। নদীপথে এলে গ্রাম-প্রবেশের যে প্রথম ঘাট, তার নাম ‘খেয়াঘাট’। স্কুলঘাট দিয়েও গ্রামে প্রবেশ করা যায়। সবচেয়ে বড়ো ও প্রশস্ত ঘাটের নাম ‘জজের ঘাট। এর কিছু দূরেই শ্মশান ও স্টিমারঘাট। জজের ঘাট থেকে শুরু করে একটি প্রশস্ত বাঁধানো রাস্তা গ্রামের হৃৎপিন্ড ভেদ করে যেন অন্য প্রান্ত পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। গ্রামের মধ্যে এই জজের ঘাটটি সর্বজনপ্রিয়। বহুবছর ধরে গ্রামের তরুণদের বৈকালিক আড্ডার আসর ছিল এটি। ডালহৌসি স্কোয়ারে টেগার্টকে হত্যার চেষ্টায় বিফলকাম যে বিপ্লবী শেষে ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়েছিল, সেই অনুজা সেন ও স্টেটসম্যান সম্পাদক ওয়াটসনকে হত্যার চেষ্টায় বিফল হয়ে যে বিপ্লবী প্রাণ দিয়েছিল–সেই অতুল সেন ও অন্যান কত সাহসী তরুণকে দেখেছি নদীঘাটের এই বৈকালিক আড্ডা থেকে বাজি রেখে হঠাৎ নদীগর্ভে ঝাঁপিয়ে পড়ে তরঙ্গসংকুল সুপ্রশস্ত ভৈরব-নদ পারাপার করছে। সে দুর্বার প্রাণচাঞ্চল্য আজ কোথায় যেন মিলিয়ে গেছে। এও মনে পড়ে নদীর অপর পারে পল্লিতে হঠাৎ একদিন নিজেদের ভেতর যখন দাঙ্গা বাধে তখন ওপার থেকে ভীত শিশু ও নারীর আর্তনাদ এপারে ভেসে আসতেই এপারের ছেলেরা নৌকার জন্যে কিছুমাত্র ইতস্তত না করে নির্বিচারে স্রোতবহুল নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওপারে গিয়ে দাঙ্গাকারীদের শান্ত করে এসেছিল। এসব ঘটনা আজ মধুর স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে।
রাজনৈতিক জীবনে সেনহাটীর নাম উল্লেখযোগ্য। সেই ‘হিন্দু স্বদেশি মেলা’র যুগের বিপ্লবী নেতা স্বর্গত হীরালাল সেন থেকে আরম্ভ করে শহীদ অনুজা ও অতুল পর্যন্ত সকলেই গ্রামে সাধারণ সরল জীবনযাপন করতেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথ একবার বিপ্লবী হীরালাল সেনের পক্ষে সাক্ষ্য দেবার জন্যে খুলনার আদালতে হাজির হয়েছিলেন। হীরালালবাবু কিছুদিন রবীন্দ্রনাথের কোনো জমিদারির ম্যানেজার ছিলেন। এই সূত্রে তাঁকে সাক্ষী মানা হয়েছিল। বিশ্বকবি বিনা দ্বিধায় সেই বিপদের দিনে বিপ্লবী হীরালালের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই মোকদ্দমায় হীরালালের জেল হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে তার পরিবারের তত্ত্বাবধানের সকল ব্যবস্থা করেছিলেন। সেনহাটীর অনতিদূরবর্তী ‘দৌলতপুর’ গ্রামে বিপ্লবী কিরণ মুখার্জি প্রতিষ্ঠিত সত্যাশ্রম’ আমাদের গ্রামের তরুণদের মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। সেখানেই অনেক বিপ্লবীর প্রথম দীক্ষা। আশ্রমটির কার্যকলাপ বাহ্যত সমাজসেবায় পরিস্ফুট থাকলেও এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের গ্রামেও অনুরূপ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। প্রবুদ্ধ সমিতি’ প্রতিষ্ঠানটি এদের অন্যতম। শহীদ অনুজা ও অতুল এই সমিতির সভ্য ছিলেন। আজ মনে জাগছে এঁদের মতো কত নিঃস্বার্থ তরুণ-তরুণীর আত্মদানে এই দেশের স্বাধীনতা এসেছে, কিন্তু তাঁদেরই, ভাই, বোনেরা সব আজ একটু আশ্রয়ের খোঁজে দিশেহারা। তাঁদের শত আবেদন-নিবেদনেও রাজমসনদে বাদশাজাদার তন্দ্রা টুটে যায় না।
বিভিন্ন শ্রেণির লোকের বাস সেনহাটী। খ্যাত, অখ্যাত বহু লোকের জন্মভূমি এই গ্রাম। দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে গ্রামের তিনটি বিশিষ্ট বাড়ি কবিরাজবাড়ি’, ‘বক্সীবাড়ি ও ডাক্তারবাড়িতে পুজোর তিন রাত্রি যাত্রাগান হত। স্থানে স্থানে শৌখিন সম্প্রদায়ের থিয়েটার হত। ‘ভেনাস ক্লাব’, ‘বান্ধব’, ‘নাট্যসমিতি’ ‘ছাত্র নাট্যসমিতি’ এ তিনটি শৌখিন নাট্য সম্প্রদায় তাদের অভিনয় নৈপুণ্যে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিল। কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি এস, আর, দাশগুপ্ত, ব্যারিস্টার নীরদ দাশগুপ্ত প্রভৃতি ‘ভেনাস ক্লাবের’ সভ্য ছিলেন। এঁদের অভিনয় কৃতিত্বের কথা আজ গ্রামবাসীরা গর্বের সঙ্গে স্মরণ করে। নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তও গ্রামের লোক। তিনিও এ গ্রামে কয়েকবার কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেছেন।
এইসব যাত্রা, থিয়েটারে কত মুসলমান হিন্দুর পাশে বসে গান শুনতেন। কত মুসলমান ‘ধ্রুব’, ‘প্রহ্লাদে’র দুঃখে বিগলিত হতেন, ‘সীতাহরণ’ দেখে ক্রুদ্ধ হতেন। আজ সেইসব সরল প্রাণ গ্রামবাসী মুসলমান প্রতিবেশীরা কোথায়? বিজয়াদশমীর দিন সন্ধ্যায় নদীর তীরে অভূতপূর্ব দৃশ্যের সমাবেশ হত। প্রায় পঞ্চাশখানা প্রতিমা সারি সারি জোড়া নৌকার বুকে বাজনার তালে তালে নেচে বেড়াত। স্টিমারে করেও অনেক দর্শক আসত প্রতিমা বিসর্জন দেখার জন্যে। অসংখ্য নৌকার বাজনাদারদের বাজনার দাপটে ও নৌকা-স্টিমারের ভিড়ে এক মাইলব্যাপী নদী-পথে ‘সামাল সামাল’ রব পড়ে যেত। সমস্ত জায়গা জুড়ে একটা নৌযুদ্ধের আবহাওয়া সৃষ্টি হত। তারপর ‘বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে’ বিষণ্ণ চিত্তে সবাই ঘরে ফিরতেন। দশমীর প্রীতি আলিঙ্গনে পরিবেশ মধুর হয়ে উঠত।
ব্যাবসায়িক জীবনেও সেনহাটীর নাম ছিল উন্নত। গ্রামটি নদীতীরে অবস্থিত বলে নানাদেশের পণ্য, বিশেষ করে সুন্দরবন থেকে আনীত বহু জিনিস এখানে ক্রয়-বিক্রয় হত। গ্রামের প্রধান বাজারটি নদীতীরেই বসত–এ ছাড়া কয়েকটি হাট সপ্তাহে দু-একদিন গ্রামের অন্যত্র বসত। ক্রেতা-বিক্রেতারা বিভিন্ন শ্রেণির হলেও কিছু সময়ের জন্যে হিন্দু-মুসলমান সকলেই মিলেমিশে এক পরিবার বনে যেতেন—’খুড়ো’, ‘ভাই’ ‘দাদা’ সম্বোধনের পরিবেশে বিভিন্ন শ্রেণিগত লোকের এরূপ আন্তরিক মিলন আর কখনো সম্ভব হবে কি না কে জানে। এই হাট-বাজারেই গ্রামবাসীদের দৈনন্দিন জীবনের অধিকাংশের সুখ-দুঃখের, আশা-নিরাশার কথা হত। সেসবই আজ স্বপ্ন বলে মনে হয়।
গ্রামের কয়েকটি প্রাচীন কীর্তি উল্লেখযোগ্য। সদ্ভাবশতক-এর অমর কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের বাড়িতে বাসুদেব মূর্তি এক অতিপ্রাচীন কীর্তি। মূর্তিটি কষ্টিপাথরের বলে মনে হয় এবং উচ্চতায় হবে দু-ফুট, মূর্তির মাথায় কিরীট, পরিধানে আজানুলম্বিত কটিবাস, গলায় কটিদেশাবলম্বী বক্ষোপবিত ও আজানুলম্বিত বনমালা। দক্ষিণাধঃ-হস্তে পদ্ম, দক্ষিণোর্ধ্বে গদা, বামোর্ধ্বে চক্র ও অপর বামহস্তে শঙ্খ এবং দক্ষিণপার্শ্বে পদ্মহস্তা শ্রী ও বাম-পার্শ্বে বীণাহস্তা পুষ্টি দন্ডায়মানা। মূর্তির পদনিম্নে গরুড় ও গরুড়ের দক্ষিণে দুটি ও বামে একটি অপরিচিত মূর্তি। এই মূর্তি কোন সময়ে, কোথা থেকে, কার দ্বারা কীভাবে আনীত হয়েছিল সে-সম্বন্ধে কিংবদন্তি আছে।
সাড়ে চারশো বছর আগে সেনহাটী গ্রামের নরহরি কবীন্দ্র বিশ্বাস কামাখ্যাধিপতির রাজধানীতে কিছুদিন দ্বারপন্ডিত নিযুক্ত ছিলেন। এই সময় তিনি কামাখ্যা মহাপীঠস্থানে উৎকণ্ঠ তপস্যা করে মহামায়ার কৃপায় লক্ষ্মীদেবীর মূর্তিসহ বাসুদেব মূর্তি লাভ করেন। কিন্তু মায়াতরীযোগে গৃহে ফিরে এসে বাসুদেবের মূর্তি পূর্বে গৃহে নিয়ে যাওয়ায় লক্ষ্মীদেবী নৌকাসহ অন্তৰ্হিতা হয়ে যান এবং কবীন্দ্র আকাশবাণী শুনতে পান–আমাকে উপেক্ষা করে তুমি আগে ঠাকুরকে ঘরে নিয়ে গেছ–আমি তোমার ঘরে আর যাব না। তুমি ঠাকুরকে ভালোবাস, তাঁকেই পূজা করো–তাতেই তোমার মঙ্গল হবে। সেই থেকে বাসুদেবের মূর্তিটি সেনহাটীতে পূজিত হয়ে আসছে।
সেনহাটীর দ্বিতীয় প্রাচীন কীর্তি ইতিহাস-বিখ্যাত মহারাজ রাজবল্লভ নির্মিত একটি শিবমন্দির, একটি রাসমঞ্চ ও তাঁর খনিত একটি দিঘি। সাধারণের চক্ষে এসবের মূল্য অল্প হলেও ঐতিহাসিকের নিকট এর যথেষ্ট আদর আছে। কারণ মোগল স্থাপত্যের আদর্শ অনুকরণে রাজবল্লভ তাঁর বাসভূমি রাজনগরকে যে-সকল কারুকার্যময় বিবিধ সৌধ, সপ্তরত্ন ও শতরত্ন নামক বিশাল বিরাট মঠাদির দ্বারা সজ্জিত করেছিলেন, কীর্তিনাশা পদ্মার বিরাট গ্রাসে পড়ে তা চিরদিনের জন্যে লোকচক্ষুর অগোচর হয়েছে। সুতরাং রাজবল্লভ নির্মিত সৌধাবলির গঠনপ্রণালী ও বাঙালির কলাকুশলতার ও স্থাপত্য নৈপুণ্যের সাদৃশ্য অনুভব করতে হলে এই দুটি থেকে তার কতক পরিচয় পাওয়া যাবে।
সেনহাটীর তৃতীয় প্রাচীন কীর্তি ‘শিবানন্দ’ ও ‘সরকার ঝি’ নামক দুটি প্রাচীন দিঘি। দ্বিতীয় দিঘিটির নামকরণ কাহিনিটি বড়োই করুণ ও মর্মস্পর্শী। এ সম্বন্ধে জনশ্রুতি এই যে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে যশোহর মৃজানগরে নূরউল্লা খাঁ নামক একজন ফৌজদার ছিলেন। তাঁর সৈন্যসামন্তের ভার ছিল তাঁর জামাতা লাল খাঁর হাতে। যুবক লাল খাঁ অত্যন্ত উদ্ধৃঙ্খল প্রকৃতির লোক ছিল। লাল খাঁর অত্যাচারে গৃহস্থ বধূগণ ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতেন। অবশেষে তার অত্যাচার চরমে ওঠে। তার পাপদৃষ্টি নূরউল্লার হিসাবনবীশ রাজারাম সরকারের বিধবা কন্যা সুন্দরীর ওপর পড়ে। তাকে লাভ করবার জন্যে লাল খাঁ নূরউল্লার অনুপস্থিতিতে বৃদ্ধ রাজারামকে কারারুদ্ধ করে–তারপরে তাঁর ওপর ভীষণ অত্যাচার করতে শুরু করে।
সুন্দরী অল্পবয়স্কা হলেও বুদ্ধিমতী ছিলেন। পিতার নির্যাতনের সংবাদ জানতে পেরে তিনি লাল খাঁর প্রস্তাবে সম্মতির ভান করে বলে পাঠালেন–”আমার পিতাকে ছেড়ে দিলেই আপনার প্রস্তাবে সম্মত হতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু তার পূর্বে আমি আমার পিত্রালয় সেনহাটীতে একটি পুকুর কাটিয়ে সাধারণের কিছু উপকার করতে চাই, আপনি সেই বন্দোবস্ত করে দিন। সুন্দরীর কথা সত্য মনে করে লাল খাঁ আহ্লাদে উৎফুল্ল হয়ে উঠল ও বহুসংখ্যক চেলার দিয়ে সুন্দরীকে সেনহাটীতে পাঠিয়ে দিল। এদিকে মৃজানগর থেকে যাবার সময় সুন্দরী পিতাকে সংবাদ পাঠালেন–’শুধু সময় ক্ষেপ করবার জন্যে এই কৌশল অবলম্বন করেছি। ফৌজদার সাহেব বাড়ি এলেই তাঁকে সব জানিয়ে মুক্ত হবার চেষ্টা করবেন। যদি মুক্ত হন তবে অবিলম্বে বাড়ি চলে যাবেন। আর যদি না পারেন, তবে শিক্ষিত পারাবত ছেড়ে দেবেন। পারাবত দেখলেই আমিও আমার সম্মান রক্ষার জন্যে যথাকৰ্তব্য করব।’
যথাসময়ে লোকজন সেনহাটীতে পৌঁছে দিঘি খনন করতে থাকে। ক্রমে বহুদিন অতিবাহিত হয়ে যায়। সুন্দরী পিতার কোনো সংবাদ না পেয়ে উৎকণ্ঠিতা হয়ে পড়লেন। এদিকে দিঘির খননকার্য শেষ হওয়ায় তা উৎসর্গের আয়োজন করা হল। এই উপলক্ষ্যে সুন্দরী যখনই ওই দিঘির জলে অবতরণ করলেন, এমন সময় পিতার শিক্ষিত পারাবতটি উড়ে এসে তাঁর কাঁধে বসল। পারাবত দেখে তাঁর প্রাণ উড়ে গেল–মুহূর্ত মধ্যেই তিনি আপন কর্তব্য স্থির করে নিলেন। নিজের মর্যাদা রক্ষার জন্যে সন্তরণচ্ছলে তিনি দিঘির গভীর জলে গিয়ে ডুব দিলেন–আর উঠলেন না!
এদিকে কিছুদিন আগেই ফৌজদার সাহেব দেশে ফিরে লাল খাঁর অত্যাচারের কথা শুনে তাকে দেশ থেকে বহিষ্কৃত করে রাজারামকে মুক্তি দিয়েছেন। কারামুক্ত রাজারাম জন্মভূমি সেনহাটীতে ফিরে আসবার অভিপ্রায়ে যখন অশ্বারোহণ করতে যাবেন–ঠিক তখনই তাঁর শিথিল বস্ত্র থেকে শিক্ষিত পারাবতটি উড়ে যায়। বিপদ বুঝে রাজারাম তখনই বেগে অশ্ব ছুটিয়ে দেন। কিন্তু যখন নিজ বাসভূমি দিঘির পাড়ে এসে তিনি উপস্থিত হলেন, তখন দেখেন সব শেষ হয়ে গেছে। কন্যাস্নেহ-কাতর বৃদ্ধ রাজারাম আর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে দিঘির জলে ঝাঁপ দিয়ে কন্যার অনুগমন করে সকল জ্বালা থেকে মুক্তিলাভ করলেন।
‘সরকার ঝি’ সুন্দরী বহুকাল এ মরধাম ত্যাগ করে গেছেন। তাঁর বাসভূমির চিহ্ন পর্যন্ত লোপ পেয়েছে। কিন্তু তাঁর খনিত দিঘি ‘সরকার ঝি’ আড়াইশো বছর ধরে গ্রাম্য বালক বালিকা, পল্লির যুবতী ও বয়োবৃদ্ধার হৃদয়ে তাঁর স্মৃতি জাগিয়ে রেখেছে–তাঁর দুরদৃষ্টের করুণ কাহিনি শুনতে শুনতে এতকাল ধরে তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু হাল আমলে শত শত সেনহাটীবাসীকে ঘর হারিয়ে যে সর্বহারা হতে হল তাদের জন্যে আজও যারা সেনহাটীতে আছে তাদের কেউ একফোঁটা চোখের জলও কি ফেলছে?
.
শ্রীপুর
বান এসেছে ইছামতীতে। জল নয়, প্রাণের বন্যা। উপনিবেশের সন্ধানে যশোহর থেকে রওনা হয়েছিল একদল লোক রাজা প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পর। সে দলের নেতা রাজা ভবানী দাস দেশ খুঁজতে এসে থমকে দাঁড়ালেন এখানে ইছামতী আর যমুনার তীরে। এদিকে সাহেবখালির একটু দূরে রায়মঙ্গল। বিস্তীর্ণ বনভূমি ছিল সেদিন। তাঁবু ফেললেন রাজা ভবানী দাস। প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠল ইছামতীর তীরভূমি। মানুষের হাতে বনজঙ্গল সাফ হল। গড়ে উঠল সুন্দর এক গ্রাম। শ্রীহীন বনভূমি মানুষের উপনিবেশে রূপান্তরিত হয়ে নতুন নাম পেল শ্রীপুর। ধীরে ধীরে মধ্যযুগের শাসন শেষ হয়ে এল শ্রীপুরে। এল ইংরেজ। বণিক-সভ্যতার আওতায় প্রকৃতির সন্তানেরা উঠল হাঁপিয়ে। গ্রামে এসে প্রবেশ করল রেলগাড়ি। কাঁচের বিনিময়ে নিয়ে গেল কাঞ্চন। শুধু শ্রীপুর নয়, বাংলাদেশের অনেক বর্ধিষ্ণু, উন্নত গ্রামই এমন করে বণিক সভ্যতার শোষণে পর্যুদস্ত হয়ে গিয়েছে। তবু বাংলাদেশের মানুষ মরেনি। শ্রীপুরও মরেনি। কিন্তু আজ ষড়যন্ত্রের চাপে বাংলাদেশেও লক্ষ গ্রামের মতো শ্রীপুর থেকেও শরণার্থীর বেশে মানুষের দল সীমান্ত অতিক্রম করে আবার আসছে নতুন উপনিবেশের আশায়। কোথায় মিলবে সে আশ্রয় কে জানে?
খেয়াঘাট থেকে কালো মাটির পথটা গ্রামের মধ্যে পাকা রাস্তায় গিয়ে মিশেছে–দু-পাশে সাজানো গাছের সারি, চর শ্রীপুর আর পাটনি পাড়ার মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে গোপখালি নদী। ছোট্ট কুলটা দূর থেকে দেখা যায়–আরও, আরও একটু দূরে ঐতিহাসিক মজুমদার বাড়ি চোখে পড়ে। এঁদের দাপটে নাকি একদিন বাঘে-গোরুতে একই ঘাটে জল খেত। মজুমদার বাড়ির কোল বেয়ে এক সড়ক চলে গেছে দাদপুরের মধ্য দিয়ে সোজা। দু-পাশে খেজুর গাছ আর ধানখেত। আর ওই তো, অদূরে পাতনার বিল-যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু বিলই চোখে পড়ে। সন্ধের পর এই বিলের ওপর দিয়ে লোক চলাচল করে না। গা ছমছম করে। রাত্রে কারা যেন ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ায় খটাখট খটাখট। বোসপুকুর আর মুচিপোতা লোকশূন্য। আজও মায়েরা ছেলেদের ভয় দেখিয়ে বলতেন, মুচিপোতার স্কন্ধকাটাকে ডাকব। চল চল বোসপুকুরধারে তোকে দিয়ে আসি। ঝোপেঝাড়ে বনেজঙ্গলে ভরে গেছে এর সবদিক সন্ধের পর যে-কোনো অতিসাহসী ব্যক্তিরও বুকটা ধড়াস করে ওঠে।
সরকার পাড়ার পাশ কাটিয়ে লাল সড়কের পথ–এপ্রান্ত হতে ওপ্রান্ত অবধি চলে গেছে। এ পথ চলে গেছে যেন কোনো এক অজানা পথের ডাক দিয়ে। সরকারদের দাপট একদিন ছিল–চৌধুরিরাও বড়ো কম যেতেন না। মিউনিসিপ্যালিটি, ডাকঘর, উচ্চ ইংরাজি ও মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়, বালিকা বিদ্যালয়, মেটারনিটি হোম, বাঁধা থিয়েটার স্টেজ কিছুরই অভাব নেই। কত ত্যাগ স্বীকারের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে এই আদর্শ গ্রাম।
একটা গ্রামে এমন শিক্ষার ব্যবস্থা, লাইব্রেরি, বাঁধানো স্টেজ, চিকিৎসালয়, ক্রীড়াব্যবস্থা আর কোথায় দেখতে পাওয়া যায়? আশা ও অনুরাগের স্বচ্ছন্দ গতিপ্রবাহ নিয়ে এগিয়ে চলছিল এই জীবন। স্যর পি. সি. রায় এই গ্রামকে গভীরভাবে ভালোবাসতেন। মাঝে মাঝে এসে তিনি বাস করতেন এখানে। তিনি ভালোবেসেছিলেন ইছামতাঁকে, ইছার জলকল্লোল তাঁকে ডাক দিত, আর এর শ্রী তাকে দিত হাতছানি–এ গ্রামেই পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ডা. বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম।
তবু চোখটা ঝাপসা হয়ে আসে কেন? দূরের রাঙাদির চরটা যেন ঝাপসা বলে মনে হয়। সাহেবখালি আর ইছামতী যমুনার সঙ্গমস্থলে দীর্ঘ মাইল চর বনজঙ্গলে ছেয়ে আছে, কেউ কেউ বলে রানিচর। গভীর রাত্রে কার যেন কান্না শোনা যায়।
অনেক পিছনে দৃষ্টি যায় ফিরে। প্রতাপের সঙ্গে যখন মোগলদের চলছিল লড়াই, জয়লাভের যখন কোনো আশাই ছিল না তখন প্রতাপের নির্দেশে নাকি সেনাপতি রডা পুরনারীদের জাহাজে করে এনে এখানে ডুবিয়ে দেয়। তারপরই এই চরের জন্ম–তাই লোকে বলে রানিচর। এ কাহিনির সত্য-মিথ্যা নিয়ে কেউ তর্ক করে না। কত, কতদিন এই চরে এসেছি, এর বনের মধ্যে পথ করে চলতে আনন্দ পেয়েছি। কত অজানা জীবজন্তুর হাড় পেয়ে অবাক হয়ে বিচিত্র পৃথিবীর কথা ভেবেছি। আরও, আরও কিছু পাওয়ার আশায় যেন অধীর আগ্রহে ছুটে চলেছি সামনের দিকে।
মেঘ জমেছে–কালবৈশাখীর প্রচন্ড দাপট বুঝি সব কিছু ভেঙে চুরমার করে দিয়ে যাবে। ভয়ে নৌকা করে পালিয়ে এসেছি তরঙ্গবিক্ষুব্ধ নদীর বুক বেয়ে। অজানা আনন্দে মনটা উঠেছে ভরে। ঝড় আসে তার অমিত শক্তিবেগ নিয়ে। নদী গর্জে গর্জে ওঠে–আছড়ে পড়ে তীরের ওপর–তীরের মাটি ধসে পড়ে নদীর বুকে–সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় নৃত্য করে নদী। কত চালা যায় উড়ে, কত জীর্ণ প্রাচীর যায় ধসে, কত বাগানে কত গাছের ডালপালা যায় ভেঙে, দুর্ভাবনার অন্ত থাকে না সাধারণের। ঝড়ের গতিবেগ ক্রমে থেমে আসে। নামে বৃষ্টি। বছরের প্রথম বর্ষা। পড়শির ছেলেরা মনের আনন্দে খেলা করে সেই জলধারার সঙ্গে। জোরে জোরে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, ‘এই বৃষ্টি ধরে যা, লেবুর পাতা করমচা।’ জেলেরা জাল কাঁধে মাছ ধরতে বেরিয়ে পড়ে। গ্রীষ্মের দাপটে অস্থির চঞ্চল মানুষের চিত্ত শান্ত হয়। ছেলেরা আম কুড়োতে বেরোয়–আমিও তাদের দলে ভিড়ে গেছি কতদিন। গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ পৃথিবী শীতল হয়। তৃষিত মৃত্তিকা জল পায়। গাছের একটা ভাঙা ডালে বসে চাতক তখন ডাকে –’দে ফটিক জল।’ কিষাণ লাঙল ঠিক করে। চাষের সময় হয়ে এসেছে। মেঘভরা আকাশ–সেদিকে চেয়ে তাদের চোখগুলো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সামনে বর্ষা!
মর্নিং স্কুল। খুব ভোরে স্কুলে যাওয়ার আনন্দ। বোসপুকুরকে পেছনে রেখে, ঘোষের বাড়ির পাশ দিয়ে সদর বিলের ওপর দিয়ে স্কুল যাওয়ার সে আনন্দ কোনোদিন ভুলবার নয়। পথে যেতে যেতে আমরা বকুল ফুলের মালা গাঁথি, কোনো কোনো দিন ছুটির পর মনে হয় : মাস্টারমশাই যেন কী? একটু দেরি হলেই কি মারতে আছে! মালা গাঁথতে যে দেরি হয়ে গেল। সূর্য তখন তালগাছের মাথার ওপর। পাগলা তালের রস পাড়ছে! মাথাভাঙা খেজুর গাছটায় বসে একটা দাঁড়কাক ডাকছে। কী যেন আনন্দ, কী যেন অনুভূতি, হঠাৎ ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরি। মা মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। আস্তে আস্তে বলেন, গ্রীষ্মের ছুটি ক-দিন দিল রে? একমাস বুঝি? হ্যাঁ, একমাস। কী আনন্দ। কাঁঠাল, আম, জাম, জামরুলের সময়। যাদের গাছ আছে তারা অনেক খাবে। আমাদের তো কোনো গাছ নেই। শিশুমন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। দূর-বোসেদের বাগানের আম রাখব নাকি? সব ঢিলিয়ে পেড়ে নেব। তাড়া করলে দে ছুট। একে তো আর চুরি বলে না?
বর্ষা আসে তার কেশপাশ এলিয়ে-দুলিয়ে। মেঘভার আকাশ, মাঝে মাঝে মেঘের ডাক– শিশুমনে ভীতির সঞ্চার করে। মেঘমেদুর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে কী আনন্দ না জাগে! অঢেল বর্ষা। এ বর্ষা বুঝি থামে না। মাঠঘাট ডুবে যায়, জলা-ডাঙা সব এক হয়ে যায়। ছেলেরা মাছ ধরতে যায়। জলে উজান নিয়ে মাছ উঠছে। মাছ ধরার আনন্দে মেতে ওঠে সবাই। বর্ষাঘন সন্ধ্যা। ঝিল্লির ডাকমুখর সন্ধ্যা। বাগানের কোনো কোণে একটা বিরহী পাখি যেন ডাকছে–বউ কথা কও। রাত্রি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে মেঘ ফিকে হয়ে আসে–ক্রমে আকাশ পরিষ্কার হয়। চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে চারিদিক। নীল নিবিড় আকাশে জ্যোৎস্নার অনন্ত উচ্ছ্বাস। সেদিকে তাকিয়ে কত কী ভাবি। আকাশের সঙ্গে মানুষের গভীর সম্পর্ক। নাড়ির সম্পর্কের চাইতেও যেন গভীর। এই সম্পর্ক অনন্ত জীবনের সঙ্গে জীবনের। নদনদী, গাছপালা সবই যেন ধরা দেয়। কবে কোন অতীতে যুগ-মধ্যাহ্নে কোন তাপস কোন বৃক্ষের তলায় তপস্যা করে হয়েছিলেন ঋষি জানি না। আবার কত মানুষ শুধু পথ চলেছে– পথ, পথ আর পথ, তাদের পথ চলার সঞ্চয় রেখে গেছে ভাবীকালের জন্যে। কত ঘুমভাঙা রাত্রি তারা জেগে কাটিয়ে দিয়েছে। মনে হয় তেমন রাত্রি যেন বারবার আসে, আসুক মহাজীবনের আহ্বান জানিয়ে–আসুক, স্বপ্নের বেসাতি নিয়ে। আসুক রঙিন ফানুস হয়ে, তবু আসুক।
চাষিরা চাষ করে। জেলেরা জাল ফেলে। পাটনিরা খেয়া পারাপার করে, কুমোররা তৈরি করে হাঁড়ি-কলসি। মধুসূদনের বাজার বসে, সবাই একহাটে এসে কেনা-বেচা করে। মাঝে মাঝে গ্রামপ্রান্তে মেলা বসে। মেলায় গিয়ে কতদিন নাগরদোলায় চড়েছি। পুতুল খেলা দেখেছি। সীতার দুঃখ দেখে চোখের জল ফেলেছি। লক্ষ্মণ-ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ দেখে অবাক বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছি। মেলায় যাত্রাগান হয়। দেশ-দেশান্তর থেকে যাত্রাদল আসে। অভিমন্যুর বীরত্ব দেখে হাততালি দিয়েছি। মনে মনে ভাবি, আমি যদি অভিমন্যু হতাম। দলু দত্তর গান শুনেছি– এম এ বি এ পাস করে সব মরছে কলম পিষে; বলি, বাঙালি বাঁচবে আর কীসে? মনের আনন্দে বাড়ি ফিরে আসি। কত আনন্দ ছিল সেদিন।
খেলার ধুম পড়ত। কেদার-মাঠে ফুটবল খেলার শেষে সবাই ইছামতীর ধারে বেলতলাঘাটে গিয়ে বসি। জ্ঞানদার দোকানে ভিড় করি। চায়ের দোকানটা ভালোই চলে। গান চলে, গল্প চলে। পশ্চিমাকাশে সন্ধ্যাতারাটা কেবলই জ্বলে। ওপারের আলো চোখে ভাসতে থাকে। ট্রেন ছাড়ার বাঁশি বাজে।
পুজোর কটা দিন চলে যায়। বিজয়ার দিন কীসের বিয়োগব্যথায় যেন সকলের চোখে জল নেমে আসে। নদীর বুকে ভাসে হাজার হাজার নৌকা বাইচ খেলা হয়; বাজি ফোটে। কত আনন্দ অথচ কত দুঃখে মানুষের মন ভারী হয়ে ওঠে। বিজয়ার শেষে সবাই আসে–সবাই আলিঙ্গন করে সবাইকে। রাত্রিতে বাড়ির ছাদে এসে দাঁড়াই। বিপ্লবী দাদাদের কথা মনে পড়ে। আজ তারা কোথায়? যিনি আমাকে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন সেই শচীন সরকারই বা কোথায়?
শীতকালের কথা বেশ মনে পড়ে।
গ্রামবাসীদের শীতের পোশাক বড়ো জোটে না। তাই ভোরবেলা তারা গাছের পাতা বিশেষ করে নোনাপাতা জোগাড় করে আনে, তাই দিয়ে আগুন করে। তারা আগুনের চারপাশে এসে ভিড় করে বসে। আগুন পোহায়।
এই গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে। আমার পূর্বপুরুষ যারা এই উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল আজ তাকে ছেড়ে যেতে হবে আবার নতুনের সন্ধানে। আবার যে নতুন উপনিবেশ গড়ে উঠবে তাকে এমনই আপনার করে আর পাব কি?
.
ডাকাতিয়া
বাংলার গ্রাম আজ কথা বলেছে; নিজের কথা, লক্ষ লক্ষ সন্তানের কথা। শুনে মনে জাগছে। আমারও জননী-জন্মভূমি ছেড়ে আসা গ্রামে’-র হৃদয় নিঙড়ানো স্মৃতি। বাংলাদেশের লক্ষ গ্রামের মধ্যে একটি গ্রাম। যেখানেই থাকি, যত দূরেই থাকি সে-গ্রামকে ভুলতে পারি না। সে-গ্রামের সঙ্গে আমার রক্তের সম্পর্ক, আমার নাড়ির টান। বহুদূরে পশ্চিমবাংলার উপান্তে এই মফসসল শহরে বসে আকাশ আর মাটির নীরব ভাষা আবিষ্কার করতে চেষ্টা করি। এখানেও গ্রামের মানুষকে আপন করে নিয়েছি। এরাও আমাকে আর শরণার্থী ভাবে না। আমি যেন এদেরই একজন। তবু কোনো এক বৃষ্টি ঝরা অলস অপরাহ্নে পশ্চিমবাংলার রৌদ্র-রুক্ষ এই অবারিত প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে মন চলে যায় বহুদূরে সেই সুদূর পূর্ববাংলায় স্নিগ্ধ ছায়ানিবিড় আমার জন্মভূমি ছেড়ে-আসা গ্রামের সেই নদী মাটি আর আকাশের আঙিনায়। মন বলে : যাই, আবার যাই।
ভাবি, আর কি ফিরে যেতে পারব না আমার ছেড়ে আসা মায়ের কোলে মা–আমার মাটির মা–সত্যিই কি পর হয়ে গেল আজ? মন মানতে চায় না। অব্যক্ত ব্যথায় ভাবাতুর হয়ে ওঠে। সহস্র স্মৃতি-সৌরভে জড়ানো মায়ের স্নিগ্ধ শ্যাম-আঁচলের পরশ কি আর এ জীবনে পাব না? লালাটে তাঁর সব ব্যথা-ভোলানো স্নেহ-চুম্বন আর কি সম্ভব নয়?
ওপার থেকে এপারে পাড়ি জমাতে হল–এ কার অমোঘ বিধান? ঘরছাড়া মানুষ কি আর ফিরবে না ঘরে–তার পূর্বপুরুষের ভিটেমাটিতে? শরণার্থীর বেশে মানুষ আসছে দলে দলে–দেহ ক্লান্ত-মন বিষণ্ণ–দু-চোখে অশ্রুর প্লাবন। জোলো হাওয়ার দেশের ভিজে মাটির সবুজ তৃণলতা এরা; শেকড় উপড়ে কঠিন মাটির দেশে এদের বাঁচাবার যে চেষ্টা চলছে তা কি সফল হবে? প্রাণরসের অভাবে শুকিয়ে যাবে না কি ভাবী যুগের সোনার ফসল?
দিগন্ত ছোঁয়া বিলের একপাশে ছোটো সেই চাষিপ্রধান গ্রাম। বিলভরা অথৈ জল। সবুজের সমুদ্র-ধানগাছের ওপর বাতাস দিয়ে যায় ঢেউ-এর দোলন। মাঝে মাঝে শাপলা কচুরিপানার ফুল; নল-হোগলা-চেঁচো বন। বিলের ওপরে ওড়ে বক, পানকৌড়ি, গাংশালিক, ক্ষণে ক্ষণে লাফিয়ে চলে গঙ্গাফড়িং।
আশ্বিন-কার্তিকে সোনার রং লাগে মাঠে মাঠে-লক্ষ্মীর অঙ্গের আভা ওঠে ফুটে। অঘ্রানে পৌষে দেবীকে বরণ করে চাষিরা তোলে ঘরে। তাঁর দেহের সৌরভে বাতাস মধুময় হয়ে ওঠে। পথে-ঘাটে-মাঠে ঘরের আঙিনায় নতুন ধানের প্রাণ-মাতানো সুবাস। ঘরে ঘরে আঁকা হল আলপনা, চলল উৎসব–নবান্ন, পৌষ-পার্বণ-নারকেল-নলেন গুড়ের গন্ধে ভুরভুর চতুর্দিক। চাষির ঘরে দারিদ্র্য আছে, কিন্তু অলক্ষ্মী নেই। দিঘল ঘোমটা-টানা ছোটো ছোটো বধূরাও জানে বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মীকে মাটির ঘরে বেঁধে রাখবার মন্ত্র। তাদের ডাগর ডাগর কালো চোখের সরল চাউনি–আজও যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে।
নৌকা-ডোঙা নিয়ে বিলের বুকে আনাগোনা করে ছেলে থেকে বুড়ো সবাই। ধরে মাছ, ধরে পাখি, কাজকর্মের অবসরে। মাছ নইলে ওদেরও মুখে অন্ন রোচে না। এপারে ফুলতলা আর ওপারে দৌলতপুর স্টেশন। রেলগাড়ির যাওয়া-আসা দেখে চাষিরা সময়ের ঠিক করে নেয়। ওরা বলে ৫টার গাড়ি, ৮টার গাড়ি, ১২টার গাড়ি। অসময়ে যায় মালগাড়ি। রেলগাড়ি চলে দেশ হতে দেশান্তরে, চাষিরা মাঠ থেকে, চাষি-বউরা ঘাট থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে যন্ত্রদানব ধূম উদগিরণ করতে করতে চলে গেল। কোথায় কোন দেশে গেল কে জানে?
রেললাইন পার হয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা সড়ক মুসলমান পাড়ার মধ্য দিয়ে চলে গেছে। জোলা পাড়ার তাঁতগুলো চলছে ঠকঠকঠক। দু-পাশ থেকে বাঁশঝাড় নুয়ে পড়ে প্রায় সারাপথটাই ঢেকে রেখেছে। বাঁশপাতা পচা একটা সোঁদা গন্ধ নাকে আসে।
‘বাবু, দ্যাশে আলেন নাহি?’–মুসলমান চাষি সহজ সৌজন্যে কুশলপ্রশ্ন করে। সৈয়দ মুনশির বাড়ির কাছে এলে ওষুধের তীব্র কটুগন্ধ নাকে আসে। উনি কবিরাজিও করেন, আবার মাস্টারিও করেন। এঁর কাছেই আমার জীবনের প্রথম পাঠ গ্রহণ। সদা হাসিমাখা মুখ–শুদ্ধ বাংলায় কথা বলেন। মাস্টারি ও কবিরাজি ওঁর উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া। ওঁর বাবা ছিলেন রহিম মুনশি, তখনকার দিনের জি. টি. পাস। দীর্ঘদেহ রাশভারী লোক ছিলেন। আমাদের গ্রামে ছোটো ছেলেপুলের কিছু হলেই এঁদের ডাক পড়ত। ভিজিটের কোনো দাবি ছিল না দেওয়ার কথা কারুর মনেও হত না। তবে বাড়ির ফলটা তরকারিটা দেওয়া হত প্রায়ই। আজও যেন তাঁদের আত্মার আত্মীয় বলে মনে হয়। হিন্দু-মুসলমান এতদিন আমরা পাশাপাশি বাস করেছি ভাই-ভাইয়ের মতন–চিরকাল সকলের সঙ্গে একটা আত্মীয়তার যোগ অনুভব করেছি। হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি জমি চাষ করেছি; এ আলের ওপর একদল খেয়েছে পান্তা –আর একদল করেছে নাশতা। কল্কে চাওয়া-চাওয়ি করে তামাক খেয়েছে। কুস্তি, খেলা, আড়ং-এ সবাই সমানভাবে অংশগ্রহণ করত–আবার কবিগান, জারিগান, গাজির গান, রামায়ণ গান–সব কিছুরই রস উপভোগ করত রাত জেগে পাশাপাশি বসে। আর আজ?
মুসলমানপাড়া ছাড়ালেই আম-কাঁঠাল-তাল-খেজুরের ভিটে পড়ে আছে। কোথা থেকে ঘুঘুর একটানা উদাস ডাক কানে ভেসে আসে। কোকিল ডাকে। কখনো-বা শোনা যায়, ‘চোখ গেল, চোখ গেল’, মন উধাও হয়ে যায় যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে। সরষে ফুলে, তিল ফুলে মাঠ গিয়েছে ছেয়ে। ফিঙে লাফায় ফুলে ভরা বাবলা গাছে। বনফুলের গন্ধে উতলা মেঠো হাওয়া দেহে বুলোয় মায়ের হাতের পরশ। দূর থেকে দেখা যায় ঠাকরুনতলা। বিশাল এক বটগাছ–অসংখ্য ঝুরি নেমেছে বিরাট বিরাট ডালপালা থেকে। সর্বজনীন দেবস্থান। গ্রামের সাধারণ ক্রিয়াকর্ম যা কিছু এখানেই হয়ে থাকে। গাজন, কালীপুজো আরও কত কী। এই ঠাকরুনতলার এক পাশে ছিল আমাদের সৈয়দ মুনশির পাঠশালা। বটগাছের শীর্ষদেশে বংশানুক্রমিক সন্তান-সন্ততি নিয়ে কয়েকটা চিল বাস করত–অন্যান্য ডালপালায় কোটরে থাকত আর সব নানা জাতের পাখি। শেষরাতে চিলের ডাকে পল্লিবধূরা রাতের শেষপ্রহর জানতে পেরে শয্যাত্যাগ করত। তারপর ছড়া, ঝাঁট, প্রাতঃস্নান প্রভৃতি থেকে দিনের কাজ হত শুরু। আর পুরুষেরা লাঙল-গোরু নিয়ে ছুটত মাঠে।
ছোট্ট গ্রাম ডাকাতিয়া। তাই বলে ডাকাত বাস করে না এখানে-কিংবা নেই তাদের কোনো অনুচর। দিগন্তপ্রসারী ডাকাতিয়ার বিল। সচরাচর এত বড়ো বিল দেখা যায় না। তার পাশের ছোট্ট এই গ্রামটি তারই নাম পেয়েছে। ডাকাতিয়ার বিলের হয়তো কোনো ইতিহাস আছে–কিন্তু আজ আর সে-কথা কেউ জানে না। তবে খালপারের মাঠে লাঙল দিতে দিতে চাষিরা নাকি অনেক সময় কোম্পানির আমলের পয়সা পেয়ে যায়। খালপারের ভিটের কাছেই একটা মজা পুকুর আছে–পূর্বে নাকি এখানেই ছিল মস্ত বড়ো এক দিঘি। পুকুরের পাড়ে একটি বড় আমগাছ আজও আছে। কয়েক পুরুষ আগে নাকি কখনো কখনো চাষিরা দেখতে পেত–দিঘির মধ্যে ছোট্ট একটা রুপোর নৌকা ভেসে উঠত–আর নৌকাটি ওই আমগাছের গুঁড়ির সঙ্গে শিকল দিয়ে বাঁধা। ওই নৌকায় মোহরভরা সোনার কলসিও নাকি ঝিকমিক করে উঠত। কিছুক্ষণ ভেসে থেকে আবার ইচ্ছামতো সে নৌকা তলিয়ে যেত দিঘির অতল কালো জলে।
বিলের ওপারে দিনের শেষে সূর্য ডোবে সোনার একখানা বড়ো থালার মতো কাঁপতে কাঁপতে। সেই সূর্যের লাল রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে দিগদিগন্তে। ছোটোবেলায় বসে বসে দেখতাম –কত যে ভালো লাগত! সূর্যাস্তের পর যখন গোধূলির স্লানিমা কাঁপতে থাকত–স্বপ্নবিহার থেকে মন নেমে আসত মাটিতে। বাঁশঝাড়ে-তেঁতুল কিংবা আমগাছে বিলে-চরা বকের ঝাঁক সাদা ডানা মেলে এসে কোলাহল করত–অসংখ্য শালিক কিচিরমিচির ডাকে কীর্তন জমিয়ে তুলত। গ্রামের মেয়েরা সাঁঝের পিদিম নিয়ে আলো দেখাত তুলসীতলায়, ধানের গোলায়, ঠাকুরঘরে। অন্ধকার নিবিড় হয়ে আসত। ঝোপেঝাপে, লতাকুঞ্জে জোনাকির ফুলঝুরি ফুটত। কোনো কোনোদিন বাঁশবাগানের মাথার ওপর যেন পথিক চাঁদ পথ ভুলে এসে তাকিয়ে থাকত।
সন্ধ্যাকালে সংকীর্তনের সুর ভেসে আসত কানে। গাঁয়ে এক সাধুর আজ্ঞা ছিল–সেখানে বাউল-কীর্তন বেশ জমে উঠত গোপীযন্ত্রের সঙ্গে। ঠাকরুনতলার স্কুলঘরে চলত গ্রামের যাত্রাদলের মহড়া। চাষি যুবকদের অশুদ্ধ উচ্চারণে বীররস প্রকাশ, স্ত্রীভূমিকায় পুরুষকণ্ঠের বিকৃত চিৎকার আজও স্পষ্ট যেন শুনতে পাই।
মেঠো পথে অন্ধকারে পথ চলছে হাটুরে লোক-হাট থেকে ফিরছে হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি ঘরকন্নার কথা বলতে বলতে। অন্যান্য বেসাতির সঙ্গে ছেলে-মেয়ের জন্যে হয়তো নিয়ে চলেছে একপয়সার বাতাসাওরা বলে ‘ফেনি’; বউ-এর জন্যে কাঁচের চুড়ি আর নিজেদের জন্যে তামাক। পরস্পরের আলাপের যোগসূত্র হল এই তামাক।
ছায়াছবির মতো কত স্মৃতির ছবি ভিড় করে আসে মনের পর্দায়। তাল খেজুর নারকেল সুপারি আম কাঁঠালের দেশ, জলকাদায় স্নিগ্ধ যার কোল, জোলো হাওয়ায় আন্দোলিত যার সবুজ আঁচল, মেঘে-রৌদ্রে হাসিকান্নায় মুখর যার গৃহাঙ্গন–সেই জন্মভূমি পল্লিমায়ের মুখখানি আজ বারবার মনে পড়ছে। ঋতু বিবর্তনের বিচিত্রতা, পল্লির সবুজ চোখজুড়ানো স্নিগ্ধতা, আকাশের প্রসারতা, দিগবলয় ঘেঁষা বিলের রহস্যময়তা আজও আমাকে নীরবে হাতছানি দিয়ে ডাকে। সোনার বাংলার লক্ষ গ্রামের সেই এক গ্রাম–তাকে আজ আমি কেমন করে ভুলি? শিশু কি কখনো মায়ের কোল ভুলতে পারে? মহাকালের নির্মম পরিহাসে মাকে ছেড়ে চলে আসতে হল দূরপ্রবাসে অশ্রুজল সম্বল করে, ওপারের মানুষ এপারে এলাম শরণার্থীর বেশে। সেই বিলের জলের মতো ছলছল করা আমার জননী জন্মভূমির চোখের জল প্রাণের গহনে যে কান্না জাগায়–কেউ কি তা বুঝবে? আমাদের সেই ঠাকরুনতলায় কালীপুজোর জন্যে সংগৃহীত ছাগশিশুদের মতো রাজনৈতিক যূপকাষ্ঠে আজ লক্ষ লক্ষ মানবশিশু বলি হতে চলেছে। কিন্তু সত্যি কি তাই হবে? ঘরের ছেলেরা কি আর ঘরে ফিরবে না?
চট্টগ্রাম – সারোয়ালি ধলঘাট ভাটিকাইন গোমদন্ডী
সুদীর্ঘ আট-দশ হাত চওড়া আরাকান রোডের দু-পাশে দেখা যায় আমার ছেড়ে-আসা গ্রামের এক বিশিষ্ট রূপ। রাস্তার দু-ধারে সারবন্দি বড়ো বড়ো গাছ–অশ্বথ, বট, আম, সোনালু আর গামার। নব কিশলয়ে ফুলে ফুলে তাদের বসন্তশ্রী মনে জাগায় সৃষ্টিকর্তার রসমাধুর্য। কৃষ্ণচূড়ার মঞ্জরি রং ধরায় মানুষের মনে, ভোরের স্নিগ্ধ বাতাস বকুলফুল কুড়োবার জন্যে ডাকে।
অদূরে ‘করেলডেঙ্গা’ পাহাড়। নিবিড় শ্যামল আস্তরণের ফাঁকে ফাঁকে নানা রঙের ফুলের সমারোহ। সোনালি রঙের সোনালু ফুল, বেগুনি রঙের গামার, বনকরবী, অজস্র কাঠ-গোলাপ ও কাঠ-মল্লিকা। পাহাড়ের গা-বেয়ে ছোটো ছোটো ঝরনা নেমে এসেছে, তার পাশে কোথাও কোথাও শণখেত। নীচে দিগন্তপ্রসারী মাঠ, বুকে তাদের নানান ফসল। তারপরই আম, জাম, সুপারি, নারকেল আর খেজুর গাছের ঘন অন্তরালে আমার জন্মভূমি কঞ্জুরি মৌজার সারোয়াতলি গ্রাম। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সময় থেকে বাইরের লোকে জেনেছে ‘সেওড়াতলি’ বলে।
কর্ণফুলির বহু শাখাপ্রশাখা গাঁয়ের ভেতর প্রবেশ করেছে। ছবির মতো তাদের রূপ তাদের প্রায় সবগুলিতেই বারোমাস নৌকা চলে।
আষাঢ়-শ্রাবণের ঘন বর্ষণেও রাস্তাঘাট ডোবে না, চারিদিক অপূর্ব শ্যামশ্রীতে ভরে যায়। পুকুর-দিঘির টলটলে জলের ওপর নানা রঙের শাপলাফুল ও পদ্মের অপরূপ সৌন্দর্যে চোখ জুড়ায়।
ভরা বর্ষায় খালেবিলে ছোটো নেংটি-পরা ছেলে-মেয়েদের মাছ ধরার হিড়িক পড়ে। এক একটি মাছ পলো চাপা পড়ার পর তাদের উচ্ছ্বসিত হাসি ও চিৎকারে প্রকৃতির সজল রূপের মাধুর্য বেড়ে যায়।
শ্রাবণ মাসের আনন্দমা মনসার আগমন। পয়লা শ্রাবণে ঘরে ঘরে মা মনসার ঘট বসে –প্রতিরবিবার ঘটের পল্লব বদলানো হয়। প্রত্যেকদিনই মনসার পুথি পড়া হয়—’বাইশ কবি মনসাপুথি’ অর্থাৎ বাইশজন কবির লেখা মনসামঙ্গল। একজন সুললিত কণ্ঠে পুথি পড়েন –কয়েকজন দোহার ধরেন। মধ্যে মধ্যে চলে গীতবাদ্য। কোনো কোনো বাড়িতে এই উপলক্ষ্যে ভোজ হয়। সংক্রান্তির দিন ঘটা করে মায়ের পুজো। পুজোয় পাঁঠা, হাঁস, কবুতর বলি পড়ে। কেউ কেউ বলি দেন আখ বা চালকুমড়ো৷
আসে শরৎ। শারদলক্ষ্মীর শুভ আগমনে প্রকৃতির সঙ্গে মানবহৃদয় আনন্দে নেচে ওঠে। ভোরবেলার শান্ত বাতাসে ভেসে আসে শিউলি ফুলের গন্ধ, দারোগাবাড়ির মঙ্গল আরতির ঘণ্টা, কাঁসর-শাঁখের পবিত্র শব্দ আর বড়োপিরের দরগা থেকে আসে সুমধুর আজান ধ্বনি।
দুর্গা পুজোয় নাগ ও মহাজনদের বাড়িতেই ধুমধাম হয় সবচেয়ে বেশি। গ্রামের প্রায় সবাই তাতে যোগ দেয়। তবে বিশেষ করে নাগেদের বাড়ির নবমী পুজোর বলি দেখবার জন্যে সারাগ্রামের লোক ছুটে যায়। বলির মোষের শিং দুটি সিঁদুরে রাঙিয়ে তার গলায় বেলপাতা ও জবা ফুলের মালা পরানো হয়। সাজতে হয় ঘাতককেও। মাথায় জবাফুলের মালার পাগড়ি, হাতে খঙ্গ–সালুপরা, সিঁদুর-রঞ্জিত সেই মূর্তিকে আজও ভুলতে পারিনি! ভুলিনি বলির পর তার ‘ঘাতক নাচ।
মনে পড়ে ছোটোবেলায় একবার বলির আগেই ছুটে পালিয়ে এসেছিলাম। বলির মোষের চোখের কোণে জলের ধারা আমার শিশুমনের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিল–আজও সেই ছবি আমার মন থেকে মিলিয়ে যায়নি।
পুজোর উৎসবের পরই মনে পড়ে ধান কাটার আনন্দের কথা। কোনো কোনো গৃহস্থের ধান কাটার সময় ঢাক-ঢোলের বাদ্য-বাজনা হত। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের আসামি তারকেশ্বরদাদের জমির ধান কাটা দেখতে জড়ো হতাম ছেলেবেলায়। খুব ভোরে বাজনদারেরা এসে সানাইয়ের তান ধরতেই দলে দলে চাষির দল জমায়েত হত। রাঙা গামছা কোমরে বেঁধে, কাঁচির ডগায় সিঁদুর লাগিয়ে সবাই রওনা হত মাঠের দিকে। মাঠজোড়া অনেক জমি, তাতে ধান কাটা চলত দিনরাত। সঙ্গে চলত বাজনা আর চাষিদের খাওয়া।
তারকেশ্বরের মা সবার বড়োমা। তিনি ধান বরণ করতেন দুৰ্বায়, বরণকুলায়, মঙ্গলঘটের জলে আর মঙ্গলপাখার বাতাসে। প্রথম আঁটি ধান এইভাবে ঘরে আনা হত। চাষিরা বিদায় পেত নতুন কাপড় ও গামছা।
চাষিদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ সব জাতই থাকত এবং তারা সবাই এইসব অনুষ্ঠান পালন করত।
চৈত্র মাসে হত ‘গৌরীর নাচ’। হিন্দু-মুসলমান সবাই এই উৎসবে যোগ দিতেন। ঢাকি-টুলি চলে মনোজ্ঞ ফুলসাজে সজ্জিত হরগৌরীর পিছু পিছু। গ্রাম হতে গ্রামান্তরে শোভাযাত্রীরা গেয়ে বেড়ায়,
আজুয়া গৌরীর মালা-চন্দন
কালুয়া গৌরীর বিয়া,
ওরে গৌরীরে নিতে আইল শিব
চুয়া-চন্দন দিয়া।…
মূল গায়েন গায় ‘আজুয়া গৌরীর…’ ইত্যাদি। পিছনে সবাই ধুয়া ধরে। বাজনার তালে তালে হরগৌরী নাচে।
ছোটো একখানা পেতলের সরাই থাকে গৌরীর হাতে। নাচের ফাঁকে ফাঁকে গিন্নিমাদের কাছে তাদের পাওনা আদায় করে।
চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিনকে বলে ‘ফুলবিষু’। এই নামকরণ অর্থহীন নয়। ফুলের মালায়, নিমপাতায় আর কেয়া কাঁঠালের ফালিতে বাড়ির দরজা-জানালা সাজানো হয়। বাড়ির সব কিছুকেই মালা পরানো হয়, এমনকী আসবাবপত্র এবং গৃহপালিত পশু-পক্ষীও বাদ পড়ে না।
চৈত্র সংক্রান্তির কয়েকদিন আগে থেকেই ঘরে ঘরে খই, চিড়া, নারকেল, তিল, চালতা, কুল ও গুড় প্রভৃতির মিশ্রণে নাড় তৈরি হয়। এই নাড়কে আমাদের চাটগাঁয় বলে ‘লাওন। সংক্রান্তি বা বিষ্ণুপর্বের দিন চলে এই ‘লাওন’ খাওয়ার উৎসব। এই উৎসবের মধ্য দিয়েই হত বর্ষাবিদায় এবং হিন্দু-মুসলমানের নববর্ষ বরণের আন্তরিক শুভকামনার বিনিময়।
জ্যৈষ্ঠ মাসে চলত আম-নিমন্ত্রণ। চট্টগ্রামের পল্লির এই এক বৈশিষ্ট্য। একে অপরকে আম খেতে নিমন্ত্রণ করবেন। নিমন্ত্রণ রক্ষা না করলে অসুখী হবেন–অনুযোগ করবেন।
মোটামুটি এই হচ্ছে আমার গ্রাম সারোয়াতলির পুজোপার্বণ।
গ্রামটি একেবারে ছোটো নয়। স্কুল, ডাকঘর ও দাঁতব্য চিকিৎসালয় আছে, আর আছে মাইলখানেকের মধ্যে কানুনগোপাড়ায় একটি প্রথম শ্রেণির কলেজ।
চট্টগ্রামের স্নিগ্ধ সুন্দর পরিবেশ তার পাহাড় ও নদীর গাম্ভীর্যের মধ্যে গড়ে-ওঠা যেসব মানুষ দেখেছি, আজ তাদের মধ্যে প্রথম মনে পড়ছে যোগেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়কে। ধনীর সন্তান, জমিদারের ছেলে, কিন্তু নির্লিপ্ত এই মানুষটি বিষয়বৈভবের কোনো খবরই রাখতেন না।
এল ভাগ্য বিপর্যয়। তিনি আপনা থেকে কেমন করে জানতে পারলেন যে, তাঁর গৃহদেবতা মা কালীর নিত্যভোগ বন্ধ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আহার বন্ধ করলেন। এরপর যে তিন মাসের মতো বেঁচেছিলেন, তার মধ্যে অন্ন আর গ্রহণ করেননি। একটুখানি হাসি দিয়ে সকলের অনুরোধ এড়িয়ে যেতেন।
তাঁকে দাদুমণি বলে ডাকতাম। কথার ফাঁকে বন্দি করে একদিন দাদুমণিকে অনুগ্রহণের অনুরোধ জানালাম। তাঁর করুণ মুখে মলিন হাসি অশ্রুরাশির মধ্যে ডুবে গেল। চুপি চুপি আমায় সব জানালেন, বললেন–ওই অনুরোধ তুই আর আমায় করিসনি ভাই।
আর আজ মনে পড়ে গ্রামের তারকেশ্বরদা ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসকে–’ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান’। মনে পড়ে–শাসকশক্তির অত্যাচারের করাল রূপ। তারকেশ্বর-রামকৃষ্ণের পরিচয় বাঙালি পাঠককে দিতে হবে না জানি, কিন্তু সেদিন গ্রামের উপর দিয়ে অত্যাচারের যে ঝড় বয়ে গেছে–সে-কথা স্মরণ করলে এখনও শিউরে উঠি।
চোখের উপর ভেসে ওঠে একদিনের নির্মম ছবি। ভোরবেলায় গভীর আতঙ্কে গ্রামবাসীর ঘুম ভাঙল-ভয়ে কারও মুখে কথা সরে না। জ্বলে উঠল তারকেশ্বর, রামকৃষ্ণ ও বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্মী প্রসন্ন সেন মহাশয়ের বাড়ি।
পুলিশ সুপার সুটার সাহেবের কতৃত্বাধীনে সারোয়াতলিকে মিলিটারির হাতে তুলে দেওয়া হল। তারা তারকাঁটা দিয়ে কালাইয়ার হাটের পাশে গ্রামের হাই স্কুলটাকে ঘিরে ফেলল। শুরু হল লাঠি-বৃষ্টি, বেয়নেটের খোঁচা ও বন্দুকের কুঁদোর আঘাত। তৃতীয় শ্রেণির শিশু থেকে দশম শ্রেণির কিশোর কেউই বাদ পড়ল না– এমনকী শিক্ষকরাও প্রহারে জর্জরিত হলেন।
এই অত্যাচার থেকে বোরলা, কানুনগোপাড়া প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিও রেহাই পায়নি। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর জালালাবাদে চলে স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহীদের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের প্রথম সশস্ত্র সম্মুখ সংগ্রাম। এই যুদ্ধের অধিনায়ক ছিলেন লোকনাথ বল। তাঁর ভাই টেগরা এবং আরও কয়েকজন সেখানে শহিদ হয়েছিলেন। তারকেশ্বর, রামকৃষ্ণের বাড়ির মতো লোকনাথদার বাড়িও ভস্মীভূত হয় সেই সময়।
তখন দেখেছি গ্রামের সকলের তাঁদের প্রতি কী সহানুভূতি ও সমবেদনা! বিদেশি শাসকের অত্যাচারে এদের মনেও বেজে উঠত বিদ্রোহের সুর।
অশিক্ষিত চাষাভুষোর দল বিদ্রোহীদের লুকিয়ে রাখতেন–তাঁদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন মুসলমান। তাঁদের ঘরের মায়েরাও ‘স্বদেশি ছেলেদের’ কত যত্নই না করতেন। তাঁদের মুখে প্রায়ই শুনতাম—’আহারে দুঃখিনীর পোয়া, তোরা আখেরে রাজা হবি। তোরার দুঃখ খোদার দোয়ায় ঘুচিব।’
শুনছি সেই রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের বাড়ি তাঁদেরই এক প্রজা জোর করে দখল করেছে। তারকেশ্বরদাদের বাড়ি নিয়েও চলেছে সীমাহীন লোভের হানাহানি। আর স্বর্গীয় প্রসন্ন সেন মহাশয়ের পরিবারবর্গ আজ উদবাস্তু, পশ্চিমবঙ্গে সরকারের আশ্রয়প্রার্থী। শুধু ভাবছি নিয়তির এ কী কঠোর পরিহাস!
কিন্তু এমনতর তো ছিল না। ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের বন্যায় শহরের বাসা হতে গ্রামে চলেছি মায়ের কাছে। বেঙ্গুরা স্টেশনে পৌঁছে দেখি, চলার পথ অথৈ জলের তলায় আত্মবিলোপ করেছে, চলাচল হচ্ছে ‘সামপানে’। কিছুদূর চলার পর সামপানও আর চলে না। হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই মাইলখানেক পথ। অবর্ণনীয় সেই দুঃখের ইতিহাস। অনভ্যস্ত পায়ে এগিয়ে চলেছি। সঙ্গে চাকর অমূল্য, তার মাথায় ভারী বোঝা। কজেই তার সাহায্য পাওয়ার আশা বৃথা।
কিছুদূর গিয়েই পড়লাম এক চোরা গর্তে। বুক পর্যন্ত ডুবে গেলাম। কাপড়চোপড় ভিজে জলে কাদায় একাকার হয়ে গেল। ঠিক এমন সময় সহাস্য মুখে এগিয়ে এলেন নুর আহম্মদদা। অতিকষ্ট করে আমায় পার করলেন সযত্নে। মাকে এসে সহাস্যে বললেন—’আখুড়ি, তোয়ার মাইয়া দি গেলাম–আঁয়ার লাই মিঠাই আন।’
মায়ের মুখের মিষ্টি হাসি–তাঁর হাতের সামান্য পুরস্কারই অসামান্য ছিল নুরদার কাছে। কিন্তু সেদিন কোথায় গেল?
কে জানে মহাকালের রথচক্রতলের এই নিষ্পেষণ কবে শেষ হবে? জানি শেষ হবে, হবে এই বিচ্ছিন্ন জাতির মিলন। বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের ভাষাগত, কৃষ্টিগত ঐক্যের মধ্য দিয়ে সেই শুভদিন আবার আসবে।
.
ধলঘাট
বৈশাখ মাস। গরমের ছুটির দেরি নেই আর। স্কুলে আসার পথে দেখে এসেছি বুড়াকালী বাড়ির ধারে দত্তদের বাগানে পাকা সিঁদুরে আম ঝুলছে। টিফিনের ছুটিতে দল বেঁধে ছুটলাম কিশোর বন্ধুদের নিয়ে। আনন্দে মত্ত হয়ে আম পাড়ছি, এমন সময় আমাদের তেড়ে এল একটি লোক ‘চোর! চোর!’ বলে। যে-যার প্রাণ নিয়ে দৌড়োলাম। কোঁচড়ে বাঁধা আমগুলো রাস্তায়, পুকুরে, ডোবায় পড়ে গেল। হাঁফাতে হাঁফাতে স্কুলের দরজায় এসে পৌঁছোলাম। দেখলাম–সেই লোকটি দাঁড়িয়ে আছে, মুখে তার দুষ্টু হাসি। সে আমায় ইশারায় ডাকলে, ভয়ে ভয়ে তার কাছে গেলাম। লোকটি স্কুলের ছেলেদের পরিচিত, নাম ‘তারা পাগলা’, রাতদিন কালীবাড়ির সামনে বসে বিড়বিড় করে কী বলে, পুকুরে একগলা জলে নেমে একটির পর একটি ডুব দেয়, তারপর ভিজে কাপড়ে উঠে এসে আবার ঢোকে কালীমন্দিরের ভেতর। কোনো কাজকর্ম নেই তার, খাওয়া-পরার ঠিক নেই, কথাবার্তায় সুস্থ মনের পরিচয় পাওয়া যায় না। স্কুলের ছেলেরা তাকে খ্যাপায়, সে ছুটে আসে তাদের মারতে।
‘তারা পাগলা’ আমায় ডাকল কেন–দূর থেকে জানতে চাইল আমার সহপাঠীরা।
অদূরে গাছতলায় বসে আমার হাতটি দেখে পাগলা বললে, এবার পরীক্ষায় তুই ‘ফাস্ট হবি, ভালো করে পড়াশুনো করিস, বুঝলি?
আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আমারই একজন সহপাঠী জিজ্ঞেস করল, আমি?
পাগলা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে, তুই সপ্তজন্মেও পাশ করতে পারবি না। কারখানার কুলি হবি তুই, তোর পড়ার দরকার কী?
তারা পাগলের কথা সত্যি হয়েছিল, সে-কথা মনে পড়ছে আজ। কিন্তু সেদিন চপল কিশোরচিত্তের হাজার কথার মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিল এই সাধকের ভবিষ্যদ্বাণী।
এই তারা পাগলাই তারাচরণ পরমহংসদেব হয়েছিলেন উত্তরকালে। তাঁর সাধনার পীঠভূমি বুড়াকালী বাড়ি পরিণত হয়েছিল হিন্দুদের পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে। সত্যের মহিমায়, সাধনার গরিমায় এই সিদ্ধ মহাপুরুষের সাধনার ক্ষেত্র ‘ধলঘাট’ এমন করে ছেড়ে আসতে হবে তা কী জানতাম!
উত্তরে আর দক্ষিণে হারগেজি খাল টেনে দিয়েছে গ্রামখানির সীমারেখা। পশ্চিমে অবারিত মাঠ মিশে গেছে দিগন্তে, পূর্বে অনুচ্চ করেলডেঙ্গা পাহাড় আকাশের দিকে চেয়ে আছে স্থির নেত্রে। চারদিকে মাঠ আর সবুজের প্রাচুর্য।
একধারে নদী বয়ে চলেছে কুলুকুলু নাদে, আর একধারে পড়ে আছে ধু-ধু মাঠ, তার বুকের উপর দিয়ে এঁকে-বেঁকে অগ্রসর হয়েছে গ্রামের বিস্তৃত পথখানি। ছায়াঘন গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় ছোট্ট কুটির, মধ্যবিত্তের মাটির দোতলা কোঠা, সানবাঁধানো ঘাট, গোয়াল, গোলা, পুকুর-দিঘি-বাগান, বাঁশঝাড়। যেন তুলি দিয়ে আঁকা। কোথাও এতটুকু আবর্জনা নেই, কোলাহল নেই, গ্রামবাসীরা মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে–মাঠে চাষ করছে চাষি, জেলে পুকুরে মাছ ধরছে, রাখালেরা বটগাছের তলায় বসে বাঁশি বাজাচ্ছে, কেউ বা খেলছে ডান্ডাগুলি, কেউ বা ব্যাটবল দিয়ে খেলছে ক্রিকেট, স্কুলের ছেলে-মেয়েরা বই বগলে করে ছুটছে স্কুলে, ব্যাঙ্কের প্রাঙ্গণে বসেছে সভা, হাসপাতালে রোগীরা দাঁড়িয়ে আছে ভিড় করে, পোষ্ট আপিসে পিয়ানকে ঘিরে বসেছে গ্রামের লোকগুলো–খোঁজ করছে চিঠির, মনিঅর্ডারের, দোকানগুলিতে জমে উঠেছে আলাপ– রাজনৈতিক, সামাজিক, ঘরোয়া। বর্ষায় যখন চারদিক জলে ভরে যায়, তখন ছবির মতো দেখায় গ্রামখানি। শরতে মাঠে মাঠে যেন সবুজের সীমাহীন রেখা, গ্রীষ্মে চোখে পড়ে ফাঁকা মাঠগুলো, বসন্তে গাছে গাছে ফুটে ওঠে নবযৌবনশ্রী।
নিরুপদ্রব একটানা জীবনযাত্রা চলেছে আবহমান কাল ধরে। বর্ধিষ্ণু আমার গ্রামখানি। কিন্তু চিরকাল তো ছিল না তার এমন উন্নত অবস্থা। আমরা যখন ছোটো ছিলাম–তখন দেখেছি আমাদের সামনের দিঘিটি জঙ্গলে আছে ভরে, রাস্তাঘাট অনুন্নত, স্কুলের গোড়াপত্তন হচ্ছে মাত্র, ব্যাঙ্ক হাসপাতালের জন্ম তখনও হয়নি। আমাদের চোখের সম্মুখে গ্রামখানি গড়ে উঠেছে।
গ্রামকে শহরের সঙ্গে প্রতিযোগিতার উপযুক্ত করে তোলার উদ্দেশ্যে ক-জন নেতৃস্থানীয় লোক এলেন এগিয়ে। তাঁদের চেষ্টায় পল্লিসংস্কার আরম্ভ হল। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে সৌন্দর্যে, শিক্ষায়, দীক্ষায় সকল বিষয়ে আমাদের গ্রামখানি হল সেরা। অভাব বলতে ছিল না কিছুরই। শহরের সঙ্গে যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত আছে, রেলপথে মাত্র চল্লিশ মিনিটের রাস্তা, জলপথেও ঘণ্টাখানেক সময় লাগে। গ্রাম, তবু শহরেরই মতো। তার চেয়ে বরং সুন্দর। গ্রামের মধ্যে অহিন্দুর বসতি নেই, কিন্তু চতুম্পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের মুষ্টিমেয় মুসলমান ও অহিন্দুরা গৌরবের সঙ্গে এই গ্রামেরই অধিবাসী হিসাবে আত্মপরিচয় দেয়।
বঙ্গবাণী, বাণীমন্দির, সাবিত্রী, শৈলসংগীত, সিন্ধুসংগীত, স্বর্গে ও মর্ত্যের রচয়িতা কবি শশাঙ্কমোহন সেনের জন্ম এই ধলঘাট গ্রামে। Star of India জগদ্বন্ধু দত্তের জন্মভূমিও ধলঘাট। দানবীর নিমাই দস্তিদার– চট্টগ্রাম শহরের Outdoor হাসপাতাল যাঁর অক্ষয় কীর্তি তিনিও এখানকারই।
ছিপ দিয়ে মাছ ধরা এ গ্রামের বৈশিষ্ট্য। কানুর দিঘিতে মাগনের দিঘিতে, ক্যাম্পের পুকুরে, পেঙ্কারদের দিঘিতে চারকাঠি বসিয়ে টঙের ওপর বসে শিকারিরা মাছ ধরে। এক একটি মাছ যেন এক-একটি জানোয়ার। ওজন দেড়মন-দু-মন। বিকেলে বঁড়শিতে আটকালে তাকে ডাঙায় তুলতে রাত হয়ে যায়। এত বড় রুই-কাতলা যে পুকুরে থাকতে পারে, এ ধারণা না দেখলে কেউ করতে পারে না।
একটা ঘটনা মনে পড়ে। শীতের দিন। কনকনে শীত পড়েছে। টঙের ওপর বসে আছি ছিপ ধরে। হাটবার ছিল সেদিন। ব্যাপারীরা, ক্রেতারা সব চলেছে দলে দলে। যেতে যেতে তারা মন্তব্য করছে, বাবুদের মাথা খারাপ, এমন শীতে কে কোথায় মাছ ধরেছে? পরিচিত লোক। বললাম, ফিরবার সময় এদিকে এসে দেখে যেয়ো কেমন মাছ ধরেছি।
বিকেলের দিকে সত্য সত্যই একটা মাছ লাগল। মন-খানেক হবে তার ওজন। বিরাট রুই। মাছটি তুলে খেজুর গাছের সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখলাম। হাট থেকে ফেরবার পথে লোকগুলো অবাক হয়ে দেখে বাড়ি ফিরল।
জমিদার এখানে নেই, আছে মধ্যবিত্ত। তারা বুকের রক্ত দিয়ে তাদের জন্মভূমিকে পুরুষানুক্রমে করেছে উন্নত। এখানে বাস করে কৃষক-যুগি-তাঁতি-মেথর-হাড়ি-ডোম–যারা শুধু নিজেদের ব্যাবসা নিয়ে পড়ে থাকে না, দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করবার সময়টুকু সকলেই করে নেয়। যারা নিরক্ষর তারাও রাজনীতি সম্বন্ধে দু-কথা বলতে পারে, সকলের এ রাজনীতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান এ গ্রামের বৈশিষ্ট্য। বারো মাসে তেরো পার্বণ এখানেও অনুষ্ঠিত হয় এ জেলার আর সব জায়গারই মতো।
গ্রামের এমন পরিবেশের মধ্যে কোথাও উদবেগ নেই, অশান্তি নেই, আছে পরস্পর সহযোগিতা, হিন্দু-মুসলমানে প্রীতি ও পল্লি উন্নয়নের সমবেত প্রচেষ্টা।
আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে যখন গ্রামখানি মাথা তুলে দাঁড়াল সকলের ওপরে, তখন হঠাৎ ব্রিটিশের রোষদৃষ্টি পড়ল গ্রামবাসীর ওপর। শহরের কাছাকাছি, মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়-প্রধান গ্রামখানি সন্ত্রাসবাদের একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠল।
গভীর রাত্রি, সূচীভেদ্য অন্ধকার। রাত্রের অন্ধকারের বুক চিরে ফুটে উঠল একটি অস্পষ্ট আলোর রেখা। তারপর গুলির আওয়াজ। একটি গুলি আমার কানের পাশ দিয়ে বোঁ করে চলে গেল। বুঝতে পারলাম না কিছুই। কিছুক্ষণ সব নীরব। তারপর একসঙ্গে শত শত গুলির শব্দ। বাইরে আসা নিরাপদ নয়, তাই ঘরে রইলাম।
সকাল হবার একটু আগে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম রাস্তায়। সশস্ত্র গুখা চ্যালেঞ্জ’ করল। দারোগা সাহেব এলেন। বললেন, রাত্রিতে নবীন ঠাকুরের বাড়িতে ঘটনা ঘটেছে, ক্যাপ্টেন ক্যামেরন সাহেব নিহত হয়েছে, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণকারীদের একজন (নির্মল সেন) আত্মহত্যা করেছেন পালাতে না পেরে।
সকালে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এলেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর সর্বপ্রথম হানা দিলেন আমাদের বাড়িতে। বললেন, আমাদের পরিবার এসব ফেরারি আসামিদের সঙ্গে জড়িত। খানাতল্লাশি হল পাড়ার পর পাড়ায়–সারাগ্রামখানিতে। তাতেও রেহাই পেল না নিরীহ গ্রামবাসীরা। চতুষ্পর্শ্বস্থ গৃহস্থের ওপর ধার্য হল পাঁচ হাজার টাকা পাইকারি জরিমানা। স্থাপিত হল চিরস্থায়ী ক্যাম্প, নির্যাতিত হল গ্রামবাসী। তবু কিন্তু এ গ্রাম ছাড়বার কল্পনা তারা করেনি কোনোদিন। পূর্বপুরুষদের ভিটের মায়া কেউ কি ছাড়তে পারে?
বাংলা বিভাগ হল। দলে দলে লোক ছেড়ে গেল তাদের জন্মভূমি। রেখে এল তাদের পূর্বপুরুষের ভিটে-মাটি। প্রথম উত্তেজনা কমে গেলেই ফিরে আসবে তারা। সবাই চলে যাচ্ছে। একা নই আমি, স্ত্রী-পুত্র-পরিবার আছে। তারা থাকতে চায় না আর। তাই বাধ্য হয়ে তাদের নিরাপত্তারই জন্যে গ্রাম ছেড়ে আসার সংকল্প করলাম। আপত্তি জানাল হিন্দু মুসলমান-বৌদ্ধ সবাই। আমিন সরিফ, আজিজ মল্ল, ফরোক আহমদ–গ্রামের মধ্যে যারা এখন মাতব্বর, একযোগে বললে, সত্যই আমাদের ছেড়ে চললেন? আমাদের এখানে তো কোনো ভয় নেই।
দুঃখ হয়েছিল তাদের কথায়। তারা তো ছিল আমার আত্মীয়েরই মতো চোদ্দোপুরুষ ধরে, পরিবারের সঙ্গে শুভেচ্ছা ও প্রীতিসূত্রে আবদ্ধ। তাদের আবার ভয় কীসের? চারদিককার অবস্থা তখন শান্ত। কিন্তু ভিড় খুব। তবু অতিকষ্টে রাত বারোটায় এসে পৌঁছোলাম শিয়ালদা স্টেশনে।
সে আজ প্রায় আট বছর আগেকার কথা। সারাদিনের কর্মব্যস্ততার শেষে যখন অপরাহু হয় তখন মনখানি ছুটে যায় আমার সেই ‘ছেড়ে-আসা গ্রামে। আমি কল্পনার চোখে দেখি আমাদের স্কুলের মাঠে ছেলেরা খেলছে মনের সুখে, বাড়ির সামনে দিঘিতে মাছ ধরতে বসেছে সুরেশ পুরোহিত, কালীবাড়িতে ওঁঙ্কারগিরির আখড়ায় ভিড় জমে আসছে। পুকুরের পোনা মাছগুলো ঘাটে এসে সাঁতার কাটছে, বাগানের মালতীলতায় টুনটুনি পাখিগুলো বসে আছে তাদের নতুন নীড়ে, ঝাউগাছে বাসা বেঁধেছে চিলেরা, গোয়ালের গোরুগুলো উঠানে ছুটোছুটি করছে, পোযা কুকুরটি দরজার সামনে বসে আছে লেজ গুটিয়ে, বিড়ালটি খাবার খুঁজে বেড়াচ্ছে এঘর ওঘর, বাগানের গোলাপ গাছগুলো ভরে আছে মুকুলে, লিচুগাছের ওপর বসে কাক মনের আনন্দে ডাকছে-কা কা। ফল-ভারে অবনত হয়েছে আম গাছের পত্রবহুল শাখা-প্রশাখা, পাকা কালোজাম বাতাসে ঝরে পড়ছে মাটিতে, রাস্তায় লোক নেই, কোথাও কোনো শব্দ নেই, চারদিকে শ্মশানের নীরবতা। সন্ধ্যা হল, কালীবাড়িতে বেজে উঠল কাঁসর-ঘণ্টা, জ্বলে উঠল আচার্যিদের বাড়িতে দু-একটি প্রদীপ, যুগিদের পাড়ায় খোল করতালে হল সন্ধ্যার বন্দনা…।
ফিরে আসতে চাইল না মন এখান থেকে। এখানকার প্রতিটি ধূলিকণার সঙ্গে যে আমার পরিচয় নিবিড়, অবিচ্ছেদ্য। এরা আমায় ডাকবে–এ তো স্বাভাবিক। কিন্তু পারি না তাদের সে ডাকে সাড়া দিতে। বোঝাতে পারি না অবাধ্য মনকে। আশা বলে, তুমি তো ছিলে না গৃহহীন, একটি বিশাল বর্ধিষ্ণু পল্লির সর্বত্রই ছিল তোমার গৃহ, তুমি তো ঘরছাড়া হতে পারো না।
ভাবি, কোনটা সত্য–আমার আশা, না আমার এ নির্মম বর্তমান?
.
ভাটিকাইন
পৃথিবীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের দিনে যে দেশের মাটিকে আপন বলে জেনেছি, যে দেশের আকাশ আর বাতাসের সঙ্গে আমার শৈশবের প্রতিটি দিনের অনুভূতি একাত্ম হয়েছিল একদিন, আজ সেই জন্মভূমির সঙ্গে শেষ যোগটুকু ছিন্ন করে চলে এসেছি। পিতৃপিতামহের ভিটে ছেড়ে দেশান্তরে পাড়ি জমিয়েছিলাম দিনের আলোতে নয়, রাত্রির অন্ধকারে। গোটা দেশটাই যেন রাত্রির তপস্যায় মগ্ন। দেশকে ছেড়েছি, কিন্তু দেশের মাটিকে তো আজও ভুলতে পারিনি। শরণার্থীর বেশে জীবনের প্রতিপদক্ষেপে আজ যে দুর্যোগের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি, এই দুঃসময়ে বড়ো বেশি মনে পড়ছে আমার জননী, আমার জন্মভূমি, আমার ছেড়ে-আসা গ্রামকে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে যাত্রা করেছি, দুঃখ বরণকেই জীবনের সহযাত্রী করে নিয়েছি, কিন্তু এই দুঃখের দিনে জন্মদুঃখিনী গ্রামের স্মৃতিকথা লিখতে বসে এখনও আশা জাগে, এখনও মন বলে, ‘সার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে।
জীবনের এক বিরাট স্থান শূন্য হয়ে গেছে বলে মনে হয়, পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে গেছে। কোথাও মাথা গুঁজবার ঠাঁই নেই। কাউকে বলবারও কিছু নেই, বললেও কেউ যেন শুনবে না। এতগুলো লোক মরেছে কি মরবে বোঝা যাচ্ছে না। বোধ হয় এরা সকলেই মরবে, আজ না হয় কাল। কেবল কৃশাঙ্গি শাখা কর্ণফুলি বেঁচে থাকবে। বর্ষীয়সীর শব্দহীন হাস্যে নিজের নিস্তরঙ্গ স্বল্প জলে কুন্ডলী পাকাবে।
নবীনচন্দ্র ‘পলাশীর যুদ্ধে’ যাদের জন্যে অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন, তারা বেঁচে আছে, তবে তারা নিজহাতে কবি ও তাঁর কাব্যকে হত্যা করেছে।
ইতিহাস ক্ষমা করবে না জানি, কিন্তু ইতিহাসের দীর্ঘ ও বিচিত্রপথে বিচরণ করে সে প্রতিঘাত উপভোগ করবার জন্যে আজকের কেউ বেঁচে থাকবে না। যে হাত আঘাত করে, সে-হাত বরাভয় দেয়, এইরূপ অসংগতি ইতিপূর্বে শোনা যায়নি। পৃথিবীর বয়স হয়েছে, বোধহয় অন্তিম দশা ঘনিয়েছে।
কিন্তু কী বলছিলাম। জীবনের এক বিরাট স্থান শূন্য হয়ে গেছে মনে হয়। যে মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম, সে-মাটি আজ আর আমার নয়, তা স্পর্শ করবার অধিকার আমার আর নেই!
চট্টগ্রাম।
একদিকে ঘন সন্নিবিষ্ট পাহাড়শ্রেণি, অন্যদিকে তরঙ্গায়িত বঙ্গোপসাগর, মধ্যে কৃষ্ণচূড়া গাছের ফুলে ভরা বিস্তৃত উপত্যকা। আজ যেন সব পুড়ে গেছে।
সীতাকুন্ড থেকে চট্টগ্রামের সে-এক অপূর্ব রূপ, যতদূর দৃষ্টি যায় কেবল পাহাড় আর পাহাড়, পাহাড়শীর্ষে শুভ্র দেবালয়ে দেবতা ‘চন্দ্রনাথ’, ক্রোড়ে প্রলয়ের প্রতীক্ষায় ত্রিশূলধারী বিরূপাক্ষ, নিম্নে নিস্তেজ স্বয়ম্ভুনাথ মর্তের মানুষের অতিনিকটে বলে রুদ্ররূপ ত্যাগ করেছেন, আরও নীচে পূতসলিলা মন্দাকিনী, অনাদিকাল হতে কলস্বরে বয়ে যাচ্ছে। পুরাণে এই স্থানটিকে চম্পকারণ্য বলা হত। উত্তরে অনাবিষ্কৃত পাহাড়-চূড়া, সহস্রধারায় জল ঝরে পড়ছে। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই এই জল পড়ে পড়ে মাটি পাথর হয়ে গিয়েছে। আবার পাহাড়গাত্রে স্থানে স্থানে অগ্নিশিখা, এর গর্জনকে স্থানীয় হিন্দুরা গুরুধ্বনি বলে। দক্ষিণে বাড়বানল। সীতাকুন্ড থেকে পাঁচ মাইল দূরে ঘন অরণ্যের মধ্যে শিববিগ্রহ ও পাতালস্পর্শী জলকুন্ড টগবগ করে ফুটছে, অথচ ডুব দিলে দেহ শীতল হয়।
চন্দ্রনাথের মন্দির থেকে এক সংকীর্ণ সর্পবহুল গিরিপথ দক্ষিণদিকে নেমে গিয়েছে। তীর্থযাত্রী দল ওই রাস্তা দিয়ে নেমে যায়। যক্ষপুরীর মতো অন্ধকার সে-পথ। পথ হাতড়িয়ে চলতে হয়। মাঝে মাঝে শাবকসহ কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যাঘ্র দম্পতিকে চলে যেতে দেখা যায়। এর নাম পাতালপুরী। স্মরণাতীতকালে কোন মহাপ্রাণ হিন্দু রাজা এই মন্দির নির্মাণ করেছিলেন জানা যায়নি। মন্দিরের অধীশ্বরী কালী, মাথা নীচে ও পা ওপরে করে পূজারিদের দিকে পিছন ফিরে আছেন। এ এক অপূর্ব মূর্তি। বহুশতাব্দী পূর্বে আবির্ভূত হয়েছেন এ দেবী, অথচ মর্ত্যের মানুষের মুখ দর্শন করেননি।
কুমিড়া, ভাটিয়ারি ও ফৌজদারির হাটছাড়াবার পর পাহাড় যেন দূরে সরে গিয়েছে। এইখানে কৃষ্ণচূড়া ফুল শোভিত ঢালু জমি। নাম পাহাড়তলি। এ. বি. রেলওয়ের কারখানা, লোকো শেড, মালগুদাম, ইঞ্জিন মেরামতের কারখানা, ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের দফতর। তারপর চট্টগ্রাম স্টেশন। গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড এখানে ঈষৎ উচ্চে, পাহাড়তলি থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত রাস্তাটা উঁচু হয়ে গেছে। বাটালি পাহাড়পার্শ্বে সংকীর্ণ গিরিপথের নাম টাইগার পাস। এইখান থেকে বড়ো পল্টন, ইউরোপীয় ক্লাব ও লাটসাহেবের কুঠি পর্যন্তও ছোটোখাটো টিলায় অসংখ্য বাংলো। আগে এখানে সরকারি বড়ো সাহেব, মার্চেন্ট অফিস ও রেলওয়ের সব বড় কর্তারা থাকতেন। আজ তাঁরা সাগর পাড়ি দিয়েছেন। যাবার আগে কার সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করে গেছেন, ইতিহাস একদিন তার বিচার করবে।
সেকালে চরচাকতাই থেকে নৌকাযোগে কর্ণফুলি দিয়ে আমাদের গ্রামে যেতে হত। প্রাচীন পল্লি ভাটিকাইন। বড়ো কর্ণফুলি ও তার নিস্তরঙ্গ শাখা ধরে সেনের পোল, সাইরার পোল, চন্দ্রকলা পোল ও ইন্দ্রপোল হয়ে এসে নুরন্নবী মাঝির নৌকা থামত, দুরন্ত বর্ষায় বড়ো কর্ণফুলির জল যখন দলিত-মথিত হত তখনও বৃদ্ধ নুরন্নবীকে অসীম সাহসে দাঁড় টেনে নৌকা নিয়ে যেতে দেখেছি। আমরা শহরেই থাকতাম, মাঝে মাঝে পাল-পার্বণে বাবার সঙ্গে গ্রামে যেতাম। ইন্দ্র পোল ছাড়িয়ে আরও দূরে নৌকা থামত। নৌকা থেকে নেমে বকাউড়া বিলে গিয়ে উঠতাম। জ্যোৎস্না রাত্রে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি ভিড় করত বকাউড়া বিলে। মাঝে মাঝে দেখা যেত হারগেজা ফুলের ঝাড় আর প্রাচীন মগেদের চিতা।
বিল ছাড়িয়ে গ্রামের রাস্তা ধরতাম। প্রথমেই শ্মশানকালীর হাট, দু-ধারে ঘন বাঁশঝাড়, বাঁশপাতা পড়ে রাস্তার কতকাংশ একেবারে ঢাকা পড়ে গেছে। গ্রামের হাই স্কুল ছাড়িয়ে আমাদের বাড়ি। গ্রামবাসী এবং নিকটবর্তী গ্রামের বহু লোক আমাদের বাড়িকে সরীর বাপের বাড়ি বলত।
সরী ওরফে সরলা আমার বড়ো পিসিমার নাম। জনশ্রুতি, সাতটি সন্তানের অকালমৃত্যুর পর পিসিমার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে এবং তিনি পিতৃগৃহে চলে আসেন। পিতৃগৃহে তখন কেউ ছিলেন না, কর্মসূত্রে সকলেই তখন চট্টগ্রাম শহরে। পিসিমা নাকি একাকী একটা বাতি জ্বেলে ভেতরের দিকের বারান্দায় অনেক রাত্রি পর্যন্ত সুর করে রামায়ণ, মহাভারত পড়তেন। অন্ধকারে মধ্যরাত্রে সেই গৌরবর্ণ দীর্ঘাঙ্গী সরলাকে চক্রবর্তীদের পোড়ো বাড়িতে একাকী ঘোরাফেরা করতে দেখে পথচারী কেউ চমকে উঠত কি না জানা যায়নি। শনি, মঙ্গলবারের মধ্যরাত্রে সরীর বাপের বাড়ির পানা-পুকুরের অভ্যন্তর থেকে প্রেত পুজার কাঁসর-ঘণ্টাধ্বনি রামায়ণ পাঠরতা সরলাকে আদৌ বিচলিত করত কি না সে সংবাদও জানা যায়নি। সকলই আজ বিস্মৃতির গর্ভে লীন। কেবল তেঁতুল ও দীর্ঘশির ইন্নালুর ডালে ডালে শাখা কর্ণফুলির উদাস বাতাস মৃত চক্রবর্তীদের নাম নিয়ে আজও লুটোপুটি খায়।
ভাটিকাইন অথবা ভট্টিখন্ড, যাই হোক-না-কেন, তাতে কিছু আসে যায় না। আমাদের গ্রামের নাম ভাটিকাইন। ভাটিকাইন থানার একমাইলের মধ্যে বহু বর্ধিষ্ণু হিন্দুর বাস ছিল গ্রামে। আমাদের বাড়ি ব্রাহ্মণপাড়ায়, হরদাসবাবুর বাড়ির পাশে। হরদাসবাবু জ্ঞানী ও ধার্মিক লোক ছিলেন। তাঁর বাড়িতে অষ্টপ্রহর কীর্তন হত। যতদূর মনে পড়ে তাঁর বাড়ির ভেতর ও বাইরের উঠোনে সংবৎসর শামিয়ানা খাটানো থাকত। উঠোন জুড়ে শতরঞ্চি পাতা, বাইরের পুকুরপাড় পর্যন্ত লোক বসত। ঝুড়ি ঝুড়ি ভোগ হত ঠাকুরের। খাঁটি গাওয়া ঘিয়ের গন্ধে সুরভিত হয়ে যেত চারদিক।
শুধু হরদাসবাবুরই যে সচ্ছলতা ছিল তা নয়, গ্রামবাসী প্রায় সকলের ঘরেই যেন লক্ষ্মী বাঁধা থাকতেন। চাল কিনে খেত এরকম লোককে লক্ষ্মীছাড়া বলা হত এবং সেরকম কেউ গ্রামে ছিল বলে জানা যায়নি।
মামার সঙ্গে কর্ণফুলিতে মাছ ধরতে যেতাম। সেজন্যে আমাদের ভাইদের আগ্রহের অন্ত ছিল না। চন্দ্র অস্ত যাবার পূর্বেই তিনি জাল নিয়ে বের হতেন। আমরা জেগে থাকতাম। মামার সঙ্গে গিয়ে ডুলা ধরব। পেছনের বাড়ির সিরাজুদ্দিন ভুঞার ছেলে বসিরও আমাদের সঙ্গে যেত। নগেন্দ্ৰকাকা, মামা, আমি, দাদা, বসির ও ওয়াজ্জারগোলার নূরমহম্মদ রাত থাকতে বাড়ি থেকে বের হতাম। বাবা বাড়ি থাকলে আমরা যেতে পারতাম না। মা কিছু বলতেন না। কেবল দিদি জেগে থাকলে সঙ্গে যাবার জন্যে বায়না ধরতেন। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তায় উঠে মরা শ্ৰীমতীর পোল পার হয়ে বকাউড়া বিলের রাস্তা ধরতাম। হঠাৎ বৃষ্টি নামলে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের চালায় গিয়ে দাঁড়াতাম। তারপর বৃষ্টির ঝাঁপটা কমে গেলে স্কুলঘর থেকে বের হয়ে ওয়াঙ্গেদারদের বাড়ি ছাড়িয়ে যেতাম। নগেনকাকা বলতেন, ওই দেখ দু মুখো ‘খাইনি’ সাপ ঘুরছে। বসির বলত ‘জঠিয়া’ সাপ। মামা বলতেন, বিলের মুখে ‘কালন্দর’ সাপ আছে। তাতেও আমরা নিরস্ত হতাম না। মরা শ্ৰীমতীর পোল পার হয়েই বিলে নামতাম। তারপর বৃষ্টির জলে, ঠাণ্ডায়, বিড়বিড় করতে করতে সকলে মিলে খালে জাল ফেলত। বাটা, হরা, পোপা, লোঠিয়া, ইচা, খোরশুলা, বেলে, গলদা ও বাগদায় নিমেষে ডুলা ভরে যেত। সকালে বাড়ি ফিরে মাছ ঢাললে উঠোনের একাংশ সাদা হয়ে যেত।
প্রতিবৎসর কাকার বাড়িতে ভাটিকাইনে যাত্রাদলের গান হত। বিজয়-বসন্ত পালা হবে। এই উপলক্ষ্যে গ্রামে সাড়া পড়ে গেছে। স্টেজ বাঁধা হয়েছে। আবদুল আজিজ মৌলবির বাড়িতে দুইটি বড়ো দেওয়ালগিরি আছে। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সেগুলি পাঠিয়ে দিয়েছেন। সন্ধ্যা থেকেই তিন গাঁয়ের লোক আসতে আরম্ভ করবেন। উঠোন জুড়ে ত্রিপল ও সতরঞ্চি পাতা হয়েছে। দেখতে দেখতে উঠোন ভরে গেল। সদরের বাইরে সাময়িকভাবে পান সিগারেট ও চায়ের দোকান বসেছে। সুদৃশ্য বালকের দল রংচঙে পোশাক পরে সখী সেজে স্টেজের ওপর গান ধরেছে—’শাখে বসি পাখি করে গান।’
বহুদিনের কথা। শঙ্খ ও হালদা নদীকে তবুও ভুলিনি। কর্ণফুলির পাশে পাশে সেগুলি আজও বয়ে চলেছে। সেই হাটহাজারি, ফটিকছড়ি, রাঙামাটির দেশ, শান্ত সমাহিত পাহাড় ক্রোড়ে নাকচ্যাপটা মগ ও চাকমা শিশুর দল। সেই চন্দ্রনাথ পাহাড়, পাতালকালীর সহস্র ধারা। সেই ভাটিকাইন যাত্রাদলের গান, চকমকে পোশাক পরে গ্রামের বড়ো অভিনেতা চন্দ্রকুমার আসরে উঠেছে। সবই মনে আছে। কিছুই ভুলিনি।…
তবে এই কলিকাতায় আমি আজ বাস্তুহারা! রিলিফ ক্যাম্পে বাস করি। ক্যাম্পে কয়েকজনের কলেরা হয়েছে। সকালে একটি বাস্তুহারা শিশু বসন্তে মারা গেছে। সে-সময়েই একমুঠো মোটা চিড়ে পেয়েছি। রিলিফবাবুর কাছে যেতে সাহস হয় না। কিছু বলতে গেলেই তিনি খেপে ওঠেন।
কেন এমন হল, সে প্রশ্ন আমি করি না। মাটির তলা থেকে মৃতের দুর্গন্ধ ওপরে ভেসে আসে কি না জানি না, জানলে হয়তো বেশি করে মাটি চাপা দিয়ে আসতাম। আসবার সময় নূরন্নবীর নাতির নৌকাখানা চেয়েছিলাম; রাতদুপুরে শ্মশানকালীর হাটের কাছে নৌকা ভিড়াতে বলেছিলাম। সেও যে বিগড়ে গেছে, আগে তা বুঝতে পারিনি। অন্ধকারে পা টিপে টিপে পটিয়া পেরিয়ে চক্রদন্ডী আসি। শেষরাত্রে হরিচরণের দিঘির ধার দিয়ে আসবার সময় কয়েকটি কুলবধূকে মরাকান্না কাঁদতে শুনেছিলাম। অদূরেই দাউ দাউ আগুন জ্বলছিল। সেই আলোয় পথ চিনে চিনেই চলে এসেছি। অনেকে আসতে পারেনি।
.
গোমদন্ডী
সৌন্দর্যের প্রতীক চট্টলা। প্রকৃতির লীলানিকেতন শৈলকিরীটিনি, সাগর-কুন্তলা, সরিক্সালিনী, কবিধাত্রী চট্টগ্রাম ভারতের জাতীয় ইতিহাসে উজ্জ্বল অক্ষরে সাক্ষী হয়ে আছে। মাঝে মাঝে জীবনসংগ্রামের তপ্ত ঝড় চট্টলার বুকে উঠলেও সে-ঝড় শান্ত হয়ে একদিন শান্তির নিবাস হয়েই দেখা দিত। সমুদ্র-ঢেউ মানুষকে ইঙ্গিত জানাত এগিয়ে চলার। স্থাণু হয়ে বসে থাকার অর্থই হল মৃত্যু-চট্টগ্রাম তাই কখনো মৃত্যুর সাধনা করেনি, সাধনা করেছে প্রাণের, সাধনা করেছে শির উন্নত করে বাঁচার মতো বাঁচার। সে মন্ত্রের পূজারি ছিল প্রতিটি মানুষ, তাই চট্টগ্রাম বিপ্লবী সৈন্যের জন্মদাত্রী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। এই চট্টগ্রামেরই বিখ্যাত কবি নবীন সেন তাই বলেছিলেন,
ভারতের তপোবন! পাপ ধরাতলে
স্বরগের প্রতিকৃতি।
সত্যিই জায়গাটি ছিল স্বর্গের মতো। ভারতবর্ষের তপোবন বলতে যদি কোনো জায়গাকে বুঝতে হয় তাহলে এই চট্টগ্রাম! আজ তার কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। বিরাট ঐতিহ্য লুপ্ত হয়েছে, বৃহদারণ্যের মৃত্যু হয়েছে। এই চট্টলারই এক নিভৃত পল্লিতে আমার জন্ম। গোমদন্ডী আমার জন্মভূমি। অখ্যাত অজ্ঞাত গন্ডগ্রাম হলেও গোমদন্ডী ঐতিহাসিক চট্টগ্রামেরই অংশ, অমৃতের উৎস। ইতিহাস থেকে যেটুকু জানা যায় তাতে দেখা যায় বর্গিদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে আমাদের পুর্বপুরুষ মাধবচন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রায় দু-শো বছর আগে বর্ধমান থেকে চট্টগ্রামে গিয়ে শঙ্খনদীর উত্তরে সুচিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। পরে সেখানে স্থানাভাব হেতুই হোক বা অন্য কারণেই হোক মাগনদাস চৌধুরি তাঁর খামারবাড়ি গোমদন্ডী গ্রামে চলে আসেন এবং নির্মাণ করেন তাঁর ভদ্রাসন। শিক্ষায় দীক্ষায় উচ্চাঙ্গের না হলেও গ্রামখানি ছিল পল্লিশ্রীর এক অফুরন্ত ভান্ডার, পশ্চিম প্রান্তে কর্ণফুলি নদীর ডাক দক্ষিণে রায়খালি খাল, উত্তরে ছনদন্ডী, খাল গিয়ে মিশেছে সূর্যাস্তের রঙে রাঙা কর্ণফুলিতে। গ্রামখানির চতু:সীমা চারটি প্রকান্ড দিঘি দিয়ে ঘেরা। প্রকৃতিদেবী পাহাড়-পর্বত, সাগর-নদী, দিঘি দিয়ে সতর্কতার সঙ্গে চট্টগ্রামকে ঘিরে রেখে শত্রুর হাত থেকে আমাদের রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে-চেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল! ঘরের মধ্যে যে বিভেদ এল, তার আঘাতেই আমরা পড়লাম ছড়িয়ে। কুসুমে কবে কীট প্রবেশ করেছিল তার সংবাদ রাখিনি, ফুলের ঘ্রাণ নিতেই ছিলাম মত্ত! মনে হয় সেই ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়েই বিষাক্ত কীট প্রবেশ করেছে মনে, তারপর কুরে কুরে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে অন্তঃকরণকে, সে-সর্বনাশের খবর পেলাম বহু দেরিতে! এত সতর্কতা সত্ত্বেও শত্রুর হাত থেকে আমরা বাঁচলাম কই? যে দুষ্ট কীট আমাদের নীচে নামিয়েছে সে-কীটের সন্ধান কি আজও আমরা পেয়েছি?
আজ গ্রামছাড়া হয়ে গোমদন্ডীকে ভাবতে ইচ্ছে করছে! মনে পড়ছে সেই ছায়াঢাকা, পাখিডাকা গ্রামখানিকে বারবার। অর্ধশতাব্দীর সুখ-দুঃখের স্মৃতিবিজড়িত গ্রামখানিকে কোনোদিন এমনভাবে ছেড়ে আসতে হবে কল্পনা করিনি, তাই বোধহয় সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির স্মৃতি ইচ্ছে করেও ভুলতে পারছি না। দিনরাত মনের এক অজ্ঞাত ক্ষতস্থান থেকে যন্ত্রণা উঠছে বুঝতে পারি, কিন্তু করার কিছুই নেই। তাই মাঝে মাঝে নির্জনে অশ্রুবিসর্জন করে মনের বেদনা ভুলতে চেষ্টা করি মাত্র।
জীবনভরা যাদের ছিল হাসি আজ কান্নাই তাদের সম্বল! দুঃখের পাঁচালি গেয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলেছি ছুটে, জানি না এ চলার শেষ কোথায়। একবার বর্গিদের হামলায় দেশত্যাগী হয়েছিলেন আমার পূর্বপুরুষ, আজ ভ্রাতৃবিরোধে আমি হলাম যাযাবর। বর্ধমান থেকে চট্টগ্রামে গেছেন পূর্বপুরুষগণ প্রাণ বাঁচাতে, আমি চট্টগ্রাম থেকে আবার বর্ধমানের কোলে এসেছি আশ্রয় এবং খাদ্যের ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে! কপালের লেখা হয়তো একেই বলে! ভাই ভাই-এর ঝগড়া যে এমন সর্বনাশী প্লাবন আনে জানতাম না। মানুষের দুর্ভাগ্য, মানুষে দীর্ঘশ্বাস শুনে ঈশ্বরকে স্বভাবতই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে,
হে বিধাতঃ! কোন পাপ করিল সে জাতি?
কেন তাহাদের হল এত অবনতি?
প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য দিয়ে ঘেরা আমার গোমদন্ডীর চারিদিকে শুধু সবুজের মেলা। ছুটি উপলক্ষ্যে শহরের কৃত্রিম পরিবেশের মায়া কাটিয়ে যখন গিয়ে পল্লিজননীর শ্যামল কোলে প্রথম আশ্রয় নিতাম তখন ভুলে যেতাম নগর-জীবনের সমস্ত দুঃখকষ্ট। জীবনের সমস্ত দৈন্য গ্লানি যেন এক মুহূর্তে ধুয়ে-মুছে যেত, পল্লিমায়ের সোনার কাঠির স্পর্শে পেতাম জীবনের নতুন সাড়া। ভাদ্র-আশ্বিন মাসে দু-কূল প্লাবিত কর্ণফুলি দিয়ে সাদা পালের নৌকায় চড়ে গ্রামে যাওয়ার সময় দু-পাশের ধানখেতে চোখ পড়লেই প্রবাসীর মন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত।
অন্ন-বস্ত্রের জন্যে নগরের যান্ত্রিক সভ্যতার চাপে যখন শরীর মন অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখনই মন বিদ্রোহ করে দেশে ফিরে যাবার জন্যে। অস্থির হয়ে পড়ি পল্লিমায়ের স্নেহশীতল ছায়ায় নির্বিঘ্ন জীবনযাপন করতে। তখনই মনে বড়ো হয়ে প্রশ্ন জাগে, আর কি ভাগ্যে জন্মভূমি দেখা ঘটে উঠবে না, আর কি কোনোদিন ফিরে যেতে পারব না আমার সেই নিভৃত কুটিরে? ছোটো ছেলেটা দেশে ফেরার বায়না ধরলে আর অশ্রু চেপে রাখতে পারি না। নিজেকে অভিশপ্ত বলে ধিক্কার দিই বার বার। মাঝে মাঝে কোনো কোনো সময় অতীতের চিন্তায় বিহ্বল হয়ে পড়লে কেবলই যেন পল্লিমায়ের স্নেহব্যাকুল আহ্বান শুনতে পাই—’ওরে আয় রে ছুটে আয় রে ত্বরা—’ কিন্তু ছুটে কোথায় যাব? পৃথিবীর আহ্নিক গতির সঙ্গে ছুটে ছুটে প্রাণ তো কষ্ঠাগত হয়ে উঠল, তবুও তো কোনো আশ্রয় মিলল না, আমাদের! শ্রমের পর বিশ্রাম না মিললে প্রাণধারণই হয়ে ওঠে অসম্ভব, কিন্তু আমরা তো শুধু শ্রমই করে চলেছি, বিশ্রামের সময় আসবে কখন?
আজ চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে গ্রামখানি উঠেছে ভেসে। মন আমার আজ বেদনাবিধুর হয়ে শুধু স্মৃতিরই রোমন্থন করে চলেছে। আমার গোমদন্ডীর বিস্তৃতি ছিল দৈর্ঘ্যে সাড়ে চার মাইল আর প্রস্থে আড়াই মাইল। বিদেশ থেকে গ্রামে চিঠিপত্রাদিতে দত্তপাড়া-দক্ষিণপাড়া, সুবৰ্ণবণিক পাড়া, বড়য়াপাড়া, বহদ্দারপাড়া ইত্যাদি বলে চিহ্নিত না করলে অনেক সময় প্রাপকের কাছে চিঠি পৌঁছে দিতে পিয়োনদের হিমসিম খেতে হত। গ্রামটিতে উচ্চ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, উকিল-মোক্তার, সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষক, রেলকর্মচারীর সংখ্যা বড়ো কম ছিল না। হিন্দু-মুসলমান খ্রিস্টান প্রভৃতি সমস্ত সম্প্রদায়েরই বাস ছিল। সপ্তপুরুষ যেখানে মানুষ সেই সোনার চেয়ে দামি আমার । গ্রামখানি আজ কোথায় গেল হারিয়ে? কোথায় গোমদন্ডী আর কোথায় আজ আমি?
সবুজধানের খেত, আম-কাঁঠালের ও সুপারিকুঞ্জ-ঘেরা বিরাট গ্রামখানির অনবদ্য শ্যামলশোভা মনকে আজও সরস করে তোলে। চারিদিকে থইথই জলে যখন মাঠ যেত ডুবে, জোয়ারের জল নদীর কানায় কানায় যখন উঠত ভরে, তখন সেই দৃশ্য দেখে আনন্দের উচ্ছ্বাসে ভেসে যেতাম। পুজোর ছুটিতে যখন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বড়ো দিঘির পাড়ে বসে পূর্বদিকের দূরবর্তী পাহাড় শ্রেণির দিকে তাকাতাম, দিঘির কাকচক্ষু স্ফটিক জলের সুদূরপ্রসারী হাওলা বিলের জলে কুমুদকহ্লার শোভিত সবুজ ধানের দোলন দেখে কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েই যেন বলেছি বহুবার,
এমন স্নিগ্ধ নদী কাহার? কোথায় এমন ধূমপাহাড়?
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্ৰ আকাশতলে মেশে?
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে?
এই স্মৃতির সঙ্গে মিশেছে শৈশবের ভুলে-যাওয়া দুষ্টুমির কথা। মনে পড়ছে ছোটোবেলায় সমবয়সিদের সঙ্গে দল বেঁধে পুকুর থেকে পদ্মফুল তোলা, জেলেদের ভাড়াটে নৌকা করে জলে-ভরা খালবিল অতিক্রম করে বেড়াতে যাওয়ার কথা, বনভোজন, খালের ওপর থেকে কাঠের পুলের রেলিং-এ বসে নানান আজগুবি গল্পগুজব, পুলের নীচে দিয়ে মাঝিদের ছই দেওয়া নৌকায় ছোটো ছোটো ঢিল ছুঁড়ে মারা, পুল থেকে ঝপাং করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়া, এমনি আরও কত কী। ফুটবল খেলার অনুশীলন উপলক্ষ্যে হাতাহাতির কথাগুলি আজও মনের মানচিত্রে জ্বলজ্বল করছে। জানি না কোন অভিশপ্ত জীবন নিয়ে আমরা সুজলা সুফলা পূর্ববঙ্গে জন্মগ্রহণ করেছিলাম, জানি না কোন বিধিবিড়ম্বনায় এমন স্বর্ণপ্রসূ জন্মভূমি ত্যাগ করে আমাদের সর্বহারা হয়ে চলে আসতে হল! কিন্তু তবু মনে হয় এ চলে-আসা আবার দেশে ফিরে যাওয়ার ভূমিকা মাত্র–আমাদের এই আশা চিরতরে আসা নয়।
মনে পড়ে বারোয়ারি পুজোর সময় ছেলে-মেয়েদের উদ্দাম আনন্দের কথা। বৃদ্ধরাও সে আনন্দের অংশীদার হতে দ্বিধাগ্রস্ত বা লজ্জাবোধ করতেন না। পুজো উপলক্ষ্যে গ্রামে থিয়েটার, যাত্রা, কবিগান, গাজীর গান ইত্যাদি শোনার জন্যে গ্রামের ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের অধিবাসীরা উৎসুক হয়ে থাকত। দূরদূরান্তর থেকে পদব্রজে এবং নৌকা করে বহু শ্রোতা আসত গান শুনতে। সে-শ্রোতার জাতিভেদ ছিল না–সেখানে হিন্দুর চেয়ে বেশি উৎসাহী ছিল মুসলমান ভাইয়েরা। সকলে সমান অংশীদার হয়ে তদারক করত আসর–গানের অর্থবোধ করে কাঁদত সকলেই সমানভাবে। সেখানে কে কার দুঃখে কাঁদছে সেটা বড়ো কথা ছিল না, বড়ো ছিল দরদি মন, বড়ো ছিল দুঃখবোধ। আজ সে নিষ্পাপ মন পরিবর্তিত, আজ অন্য সম্প্রদায়ের দুঃখে অশ্রু বিসর্জন করা যেন লজ্জার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন এমনটি হল? কেন মানুষ তার দরদ হারিয়ে অমানুষে পরিণত হয়েছে, কেন গড়ে তোলা হল বিপদের এই বেড়াজাল? এ বিপদের বেড়াজাল কি ছিন্ন করা যায় না সমস্ত দুঃখিত অবহেলিত মানুষের সামগ্রিক চেষ্টায়? মনে পড়ে দক্ষিণপাড়ার সুন্দরবলী, গোলামনকী ওরফে নকীবলী, ফতে আলি, গোপী চৌধুরি, ভৈরব দত্ত, তারিণী দে, কালী সিং, প্যারী সিং, রামগতি সিং ইত্যাদি পালোয়ানদের অদ্ভুত সব গল্পের কথা। সুন্দরবলীর বহু শক্তির কথা আজও লোকের মুখে মুখে শোনা যায়। সে নাকি প্রায় চল্লিশ বছর আগে যৌবনে পথের মধ্যে ঝড়ে নুয়েপড়া দুটি কাঁচা বাঁশ মুচড়িয়ে গ্রন্থি দিয়ে পথের পাশে সরিয়ে রাস্তা চলাচলের বিঘ্ন দূর করে দিয়েছিল। আর একবার বাড়ি থেকে নৌকাযোগে কর্ণফুলি নদী পার হওয়ার সময় মুসলমান মাঝির সঙ্গে দাঁড় টানা নিয়ে বাদানুবাদ হওয়ার পর অগত্যা নিজে দাঁড় টানতে বসে এবং দু-চারটে টান দেবার পরই অমন মজবুত দাঁড় পাটকাঠির মতো ভেঙে দু-টুকরো হয়ে যায়! এর ফল হয় আরও ঘোরালো, মাঝি প্রচন্ড রেগে অকথ্য গালাগালি দিয়ে অন্য দাঁড় টানতে বাধ্য করে তাকে। আস্তে আস্তে সুবোধ বালকের মতো দাঁড় টেনে তীরে পৌঁছে ক্রুদ্ধ সুন্দরবলী মাঝিকে একটু শিক্ষা দেবার অভিপ্রায়ে মাঝিসমেত নৌকাটি দু-হাতে তুলে কূলে উঠে পড়তেই মাঝির অন্তরাত্মা খাঁচা ছাড়ার উপক্রম হয়। ঈশ্বরের নাম জপতে জপতে সে সুন্দরবলীর হাতে-পায়ে ধরে কোনোক্রমে সে-যাত্রা রক্ষা পায়! আর সব মল্লবীরদেরও অনেককে আমি নিজের চোখে দেখেছি, তাদের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ ছিল সমান। চেহারা দেখলে চোখ ফেরানো যেত না। হাতের থাবা ছিল বাঘের মতো। বাক্যবলের চেয়ে তারা বাহুবলেরই ছিল পূজারি। গোপী চৌধুরি এত স্বাস্থ্যবান ছিল যে মাইল পঞ্চাশেক সে অনায়াসেই হেঁটে পাড়ি দিত অম্লান বদনে। আজ তারা কোথায় জানি না, কিন্তু সেদিন তারাই ছিল গ্রামের প্রহরী, গ্রামের রক্ষাকর্তা। তারা থাকতেও গ্রামের মধ্যে বিভেদ, বাইরের লোকের চক্রান্ত প্রবেশ করল কী করে? মল্লবীরদের মধ্যে তো কোনোদিন জাতিভেদের কুৎসিত হানাহানি দেখিনি। তাদের নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তা ছিল এক ওস্তাদের শিষ্য বলে। কোথায় সুন্দরবলী, কোথায় গোপী চৌধুরি? বিপদের দিনে তারা কি ‘গুরুজি কী ফতে’ বলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাম্প্রদায়িক পশুটার গলা টিপে ধরতে পারত না?
গ্রামের জাগ্রতা দেবী জ্বালাকুমারীর মন্দিরে ভক্তিভরে কতশত ভক্ত হত্যা দিয়েছে প্রাণ নিঙড়ানো অর্ঘ্য দিয়েছে। তিনিও কি জ্বালা নিবারণ করতে পারেন না আজকের মূঢ় মানুষের? কেন সবাই নির্বাক, কেন শান্তির সপক্ষে কারও স্বর উঠছে না আজ?
বছর পঞ্চাশ পূর্বে বহু শ্রমসহকারে ‘সুহৃদ পাঠাগার’ নামে একটি পাঠচক্র স্থাপন করেছিলাম, আজও মন পড়ে আছে সেই পাঠাগারে। এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন সত্তর বছরের বৃদ্ধও রয়েছেন বেঁচে, তিনি আজও গ্রামের মাটিতেই আটকে রয়েছেন খবর পেয়েছি। মাটির মায়া তাঁকে অবশ করে রেখেছে, তাঁর মতো দেশপ্রাণের সাক্ষাৎ আজ ক-জনের মধ্যে দেখতে পাই?
রেলস্টেশন থেকে জেলা বোর্ডের রাস্তাটি সোজা চলে গিয়েছে পোপাদিয়া গ্রামের বুক চিরে কালাচাঁদ ঠাকুরবাড়ির কোল ঘেঁষে আশুতোষ কলেজ পর্যন্ত। গ্রামটি দিঘিবেষ্টিত, বড়ো দিঘিতে জেলেরা যখন বড়ো জাল ফেলে মাছ ধরত সে-দৃশ্য দেখতে পুকুরপাড়ে জমত উৎসুক দর্শকের দল। তার ঘাটে সন্ধেবেলায় বসত মজলিশ, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করার আড়া। কোথাও দেখা না পেলে শেষে পুকুর ঘাটে জমায়েত হলেই নির্দিষ্ট জনের সাক্ষাৎ অবশ্যই মিলত। দু-পাশে ফুলভারে নত কামিনী ফুলগাছের ডাল এসে গায়ে লাগত, ঘাটের ওপর ঝাঁকড়া চাঁপাফুলের গাছটি গন্ধ বিতরণ করত চতুর্দিকে। বড়ো মনোরম ছিল জায়গাটি। পুকুরের পূর্বপাড়ে পিতৃপুরুষের মহাবিশ্রামের স্থান শ্মশানঘাট। শুভকাজ উপলক্ষ্যে বাড়ির বাইরে গেলে ওই শ্মশানের উদ্দেশে পিতৃপিতামহদের প্রণাম জানিয়েছি কত। তাঁদের মৃত্যুর দিনটিতে স্মৃতিস্তম্ভের পাদদেশে ফুলগুচ্ছ ও প্রদীপ জ্বালিয়ে স্মরণ করেছি বছরের পর বছর। আজ শ্মশান বলতে আলাদা কিছু বোঝায় না, সমস্ত দেশটাই শ্মশানে পরিণত হয়েছে। দূর থেকে তাই প্রণাম জানাচ্ছি শ্মশানেশ্বরকে! কোন ভগীরথ প্রাণগঙ্গা এনে অভিশপ্ত মৃত্যুপথযাত্রীদের জীবিত করে তুলবেন আজ?
পাশের বাড়ির পিসিমার প্রিয় বাঁহাস (লাউয়ের খোসার জলপাত্র) থেকে গ্রীষ্মের দুপুরে কখনো চেয়ে কখনো চুরি করে টকজল খেয়ে কতদিন বকুনি সহ্য করেছি ভেবে হাসি পাচ্ছে। পিসিমা আর বকতে আসবেন না, তিনি চিরনিদ্রায় অভিভূত। আমরা তাঁর বাগান থেকে প্রাণভরে গোটা নির্জন দুপুরে কাঁচা আম, পাকা মিষ্টি আম, আমড়া, কাঁঠাল, কামরাঙা, লিচু, কালোজাম, গোলাপজাম, জামরুল, তরমুজ, ফুটি, নোনা, আতা, শসা ইত্যাদি খেতাম ইচ্ছেমতো। অতীতের স্বাদ আজও ভুলিনি, কিন্তু সেসব ফল এখন আর তেমন করে পাব কোথায়? আজ যেন ‘উত্থায় হৃদিলীয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ’র মতো অবস্থা আমাদের, ভালোমন্দ জিনিস খাবার ইচ্ছে থাকলেও উদাসীনতার ভান করে আত্মদমন করতে হয়!
গ্রামের চারণকবি রূপদাস কৈবর্ত বা প্রসিদ্ধ কবিয়াল রমেশ শীলের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। শ্রাবণ মাস থেকে নাগসংক্রান্তি পর্যন্ত তারা মনসামঙ্গল থেকে গাথা গেয়ে সমস্ত গ্রামটিকে মুখরিত করে রাখত। মেয়েদের মধ্যেও কেউ পুজোর সময় চন্ডীমাহাত্ম্য বা জাগরণ পুথিও সুর করে পড়ত বলে মনে পড়ে। সেদিনের সেই উৎসাহ উদ্দীপনা আজ গেল কোথায়? আর কি ফিরে পাব না গ্রামের জীবন? নগরজীবনকেই কেন্দ্র করে যন্ত্রবৎ বেঁচে থাকতে হবে আজীবন? আর কি কোনোদিন শিবের গাজন, চড়কের মেলা, বারুণী স্নান উপলক্ষ্যে গ্রামে হুটোপুটি করতে পাব না? পাব না কি মুখোশ এঁটে মহিষ, বাঘ, ভাল্লুক সেজে মুখোশ অভিনয় করতে গ্রামের মাঠে? বিশ্বাস আছে মা আবার আমাদের কোলে টেনে নেবেন এবং এ নহে কাহিনি, ‘এ নহে স্বপন, আসিবে সেদিন আসিবে।’ আমরা সেইদিনের প্রতীক্ষাই করব।
জলপাইগুড়ি – বোদা
সুখের স্মৃতি বেদনা আনে, তবু যা একদিন নিতান্তই আপন ছিল অথচ রাজনীতির খেলায় যার সঙ্গে সম্পর্ক আজ অতিদূর হয়ে গেল তার কথা না ভেবে পারি কী করে! আমার গ্রামজননী বোদা বাংলাদেশের অসংখ্য গ্রামের একটি। হয়তো খুব করে বড়ো মুখে বলবার মতোও কিছু নেই তার–তবু আমার কাছে জননীর মতোই সে অদ্বিতীয়া।
চোখ মেলেই যার আকাশ দেখেছি, যার ধুলো গায়ে মেখে বড়ো হয়েছি সেই বোদা আজ পরদেশ। জানি না আজও মাঘী পূর্ণিমায় বোদেশ্বরী মন্দিরে মহোৎসব হয় কি না, স্বচ্ছতোয়া করতোয়ার উত্তরবাহী অংশে বারুণি-স্নান উপলক্ষে একমাসব্যাপী মেলা বসে কি না তাও জানি না। অম্বিকাসুন্দরী কারকুন যে শিবমন্দির স্থাপন করেছিলেন সেখানে আজও নিত্য পুজো হয় কি না সে খবরই বা আমায় কে দেবে।
বোদা যেতে হলে ডোমার পর্যন্ত যেতে হত ট্রেনে, সেখান থেকে গোরুর গাড়িতে একুশ মাইল পাড়ি দেবার পর বোদা। আরও একটা পথ ছিল। জলপাইগুড়ি থেকে চিলাহাটি পর্যন্ত ট্রেনে, সেখান থেকেও আবার গোরুর গাড়ির সাহায্য নিয়ে পনেরো মাইল পার হয়ে গেলে বোদার দেখা মিলত। জলপাইগুড়ি থেকে বোদা পর্যন্ত বাস চলা শুরু হয় আজ থেকে বছর পঁচিশ আগে। প্রথম বাসটির নাম মনে আছে, ‘আঁধারে আলো। সত্যি যেন সে বাসটি আলো হয়ে এল বোদার অধিবাসীদের কাছে।
বোদার নামকরণের ইতিহাস বলি। বুদ্ধরাজা এক বিরাট গড় তৈরি করে রাজবাড়ি স্থাপন করলেন। দু-বর্গ মাইল এলাকা। ক্রমে সেই গড়ে স্থাপিত হল দেবী বুধেশ্বরীর মন্দির। শক্তির ভ্রামরী মূর্তি দেবী বুধেশ্বরী। একান্ন পীঠের অন্যতম। ক্রমে লোকের মুখে মুখে দেবী বুধেশ্বরীর নাম হল বোদেশ্বরী। সেই থেকে ‘বোদা।
আগে রংপুর জেলায় তেঁতুলিয়া মহকুমার মধ্যে ছিল বোদা। ১৮৬৯খ্রিস্টাব্দে গঠিত হল নতুন জেলা জলপাইগুড়ি। তখন বোদা এল জলপাইগুড়ির মধ্যে। তারপর এল ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট। র্যাডক্লিফের রায়ে বোদা পড়ল গিয়ে পাকিস্তানে। আমাদের ছেড়ে আসতে হল জন্মভূমিকে।…তবু মাকে ছেড়ে আসা কি সহজ কথা?
মনে পড়ছে পোহাতুর মায়ের কথা। সেই নিরক্ষরা কৃষক জননীর ছড়া কাটা,
ছাড় জায়গা নারয় পানি,
ছাড় পুত্র না ধরে বাণী,
ছাড় দেশ নিবন্ধুয়া,
ছাড় ভার্যা দুচারিণী,
পোহাতু গামছা দিয়ে কপালের ঘাম আর চোখের জল মুছলে। বলল, মাকে কি ছাড়া যায়? মা রুদ্ধকণ্ঠে বললে,
ছাড় খেচখেচি মাও,
ছাড় খেচকেটা দাও।
ভাবছি, আমার বোদাও কি আজ নিবন্ধুয়া দেশ হয়ে উঠল? তাকেও কি শেষপর্যন্ত ‘খেচখেচি’ মায়ের মতোই ত্যাগ করতে হল?…ত্যাগ করতেই হল বোদাকে। তবু ভুলতে পারি না বোদার কথা। …কোনোদিন কি পারব ভুলতে? মনে পড়ছে সারারাত ব্যাপী যাত্রার কথা। রাতের পর রাত, পালার পর পালা।
আরও মনে পড়ছে আমন ধান রোপণের আগে গছর পোনা, ধান কাটার আগে লক্ষ্মী পুজো, আর জমিতে ধুলো ছড়িয়ে ছড়া কাটা,
আগ শুয়োর হঠ
পোকা-মাকড় দূর যাউক,
সবার ধান আউল ঝাউল,
আমার ধান শুদ্ধ চাউল।
তারপর নয়া-খাওয়া, বিশুয়া, কইনাগাত, জিতুয়া। সবই মনে পড়ে আজ।…
গ্রামের লোকসংগীতের সুর এখনও কানে বাজে। চোখ বুজে সেই সুর শুনতে শুনতে আবার আমি বোদায় ফিরে যাই। লোকসংগীত সংগ্রহের শখ ছিল খুব। গাঁয়ের মানুষের মুখে গান শুনেই তৃপ্তি হত না, তাদের কাছে বসে সেই গানের কথা লিখে নিতাম। সে কথায় কৃত্রিমতার লেশমাত্র নেই, তার সুরের উৎস হৃদয়ে। আজও ইচ্ছে করে সেই সুর শুনতে, সেই গানের কথা সংগ্রহ করতে। কিন্তু আজ তো সে দুয়ার একরকম বন্ধ।
বিশেষ করে মনে পড়ে রাখালমেয়ের মুখের মইশাল গান,
মইশাল মইশাল করো বন্ধু রে
(ওরে) শুকনা নদীর কূলে হে,
মুখখানি শুকায়ে গেছেচৈত মাইস্যা ঝামালে।
প্রাণ কান্দেম ইশাল বন্ধু রে।
আমার বাড়িতে যাইয়ো বন্ধু রে এই না বরাবর,
খেজুর গাইছা বাড়ি আমার
পুব দুয়ারা ঘর।
প্রাণ কান্দে মইশাল বন্ধু রে।
আমার বাড়িতে যাইয়ো বন্ধু রে,
বসবার দিব মোড়া,
জলপান করিতে দিব ও শালি ধানের চিড়া।
প্রাণ কান্দে মইশাল বন্ধু রে।
শালি ধানের চিড়া দিব রে বিন্দু ধানের খৈও
(আজি) মোটা মোটা সফরী কলা গামছা
পাতা দৈও রে।
প্রাণ কান্দে মইশাল বন্ধু রে।
মইশাল বন্ধুর জন্যে মেয়ের প্রাণ কাঁদছে। চৈত্রমাসের উত্তাপে শুকনো নদীর কূলে মুখখানি শুকিয়ে গেছে একেবারে। মেয়ে বলছে মইশাল বন্ধুকে, তুমি এই পথ ধরে আমার বাড়িতে যেয়ো। আমার পুব দুয়ারি ঘর, বাড়িতে আছে খেজুর গাছ। তোমার বসবার জন্যে মোড়া দেব, জলপান করতে শালি ধানের চিড়া দেব। আর দেব বিন্দু ধানের খৈও, মোটা মোটা সফরী কলা আর ঘন দই।
বোদা হল দিঘির দেশ। কত যে দিঘি! রাজার দিঘি, ময়দান-দিঘি, কইগিলা-দিঘি, ঠাঁটপাড়া-দিঘি। আরও কত দিঘি। সুউচ্চ পাড় আর অশ্বথ ছায়ায় ঘেরা ময়দান দিঘির কাকচক্ষু জলে আজও লাল শাপলার ছায়া কেঁপে কেঁপে ভাসে কি না কে জানে! ঠিক তেমনই আজও কেউ জানে না সেই লোভী ব্রাহ্মণের নাম, যে নাকি দিঘি-ঠাকুরানির ঋণ পরিশোধ করেনি।
মেয়ের বিয়ের ব্যয়বহনে অক্ষম কোনো গরিব লোক ময়দান-দিঘির পাড়ে এসে করজোড়ে প্রার্থনা জানালে জলের বুকে নাকি ভেসে উঠত মোহরে ভরতি থালা আর চালুনি। চালুনির মোহর নিলে ফেরত দিতে হত না। চালুনির মোহর ছিল দিঘি-ঠাকুরানির দান। কিন্তু থালার মোহর ভেসে উঠত ঋণ হিসেবে। এক লোভী ব্রাহ্মণ চালুনি আর-থালা, দু-পাত্রেরই মোহর আত্মসাৎ করল। কিন্তু ঋণের মোহর আর পরিশোধ করতে পারল না। শোনা যায়, সেই থেকে নাকি দিঘি ঠাকুরানি আর কাউকে দয়া করেননি।
লোকে বলে যে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় কোচবিহারের মহারাজা দুর্ভিক্ষের হাত থেকে প্রজাদের বাঁচাবার জন্যেই এইসব দিঘি কাটিয়েছিলেন। দিঘি খননের জন্যে লোকে মজুরি পেত মাথাপিছু একসের চাল আর নগদ দু-আনা।
বোদাতে শুধু দেবমন্দির আর দিঘিই ছিল না। এই ছোটো গ্রামটিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব বোধ করেনি কেউ। বোদার ছেলেদের হাই স্কুল অতিপুরোনো। মেয়েদের জন্যেও ছিল আদর্শ বালিকা বিদ্যালয়। আমগাছের ছায়াস্নিগ্ধ প্রাঙ্গণে বালিকা বিদ্যালয়টি সত্যিই পঠন পাঠনের পক্ষে ছিল আদর্শ স্থান। এ ছাড়া বরিশাল জেলার রাজবন্দি গোপালকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন একটি নৈশ বিদ্যালয়।
বোদার গৌরবের ভূষণ ছিল কোচবিহার-কাছারি। তা ছাড়া দাঁতব্য চিকিৎসালয়, জনস্বাস্থ্য কেন্দ্র, সাব-রেজিষ্টারি অফিস, থানা, ডাকঘর সবই ছিল বোদা গ্রামে।
আজও হয়তো সবই আছে। নেই শুধু আমরা–বোদার এই হতভাগ্য সন্তানেরা, ভাগ্যের পরিহাসে পশ্চিমবাংলার তথা ভারতের নানা প্রান্তে যারা আজ ‘বাস্তুহারা বলে পরিচিত। বোদাকে আজ স্পর্শ করতে পাই না, তার বাতাসে আর নিশ্বাস নিতে পাই না, তবু তাকে স্মৃতিতে পাই। বোদা আজও আমায় ডাকে। তার প্রাণের কান্না প্রতিমুহূর্তে শুনতে পাই। নাকি আমারই প্রাণের কান্নাকে তার প্রাণের কান্না বলে ভুল করি! কাঁদি, তবু ভাবি, এ কান্না একদিন শেষ হবেই, বোদার কোলে আবার গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব।
ঢাকা জেলা – বজ্রযোগিনী সাভার ধামরাই খেরুপাড়া ধামগড় আনরাবাদ শুভাঢ্যা নটাখোলা সোনারং
কর্মমুখর নগরজীবনের এক সন্ধ্যায় সম্ভাষণ এল এক বাল্যবন্ধুর কাছ থেকে। বন্ধু শুধু বন্ধুই নয়, যে আমার শিক্ষাজীবনের সহপাঠী, কর্মজীবনের সহযাত্রী। তার ডাকে পরমআগ্রহ নিয়ে গেলাম তার কাছে। সবেমাত্র সে ফিরে এসেছে আমাদের দুজনেরই জন্ম-গ্রামের কোল থেকে। দেখা হতেই প্রশ্ন : তোমার জন্যে দেশ থেকে এনেছি এক পরমসম্পদ, বলো তো সে কী হতে পারে? ভাবতে চেষ্টা করলাম শতাব্দীর সন্ধিকালে এমন কী সম্পদ সে নিয়ে আসতে পারে দূরান্তরের সেই গ্রাম থেকে। শেষপর্যন্ত সবাইকে বিস্মিত করে দিয়ে বন্ধুটি তুলে দিল আমার হাতে এককৌটো মাটি। আমার পিতৃ-পিতামহের আশিস-পূত বসতবাটি ‘বসু বাড়ির ভিটে’-র মাটি। এ মাটি আমার মা। এ মাটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে পূর্বপুরুষের পুণ্যস্মৃতি। আমার কাছে এ শুধু মহামূল্যই নয়–অমূল্য। মাথায় ঠেকালাম সে-মাটি। এ মাটি ধুলো নয়। এ মাটি বাংলার হৃদয়-নিংড়ানো রক্তে সিক্ত আজ। তার দহনজ্বালায় সর্বংসহা ধরিত্রীর চোখ থেকেও ঝরছে অশ্রু-বহ্নি। জলে ঝাপসা হয়ে এল দৃষ্টি। কেঁদে উঠল, অসহায় মন।
উত্তরে ধলেশ্বরী, দক্ষিণে প্রমত্তা পদ্মা। মাঝখানে বহুর মধ্যে এক এই গ্রাম। বর্ষার প্লাবনে খরস্রোতা নদীর ঢেউ দোলন লাগিয়ে যায় আমার গ্রামের স্নিগ্ধ মাটির বুকে। বর্ষার বিক্রমপুরের রূপ অপরূপ! জলে জলময় ছল-ছল সব পল্লি। একবারের কথা বিশেষ করে মনে পড়ে। একেবারে ছেলেবেলাকার কথা। ঘরে ঘরে সাঁকো। এবাড়ি-ওবাড়ি যেতে আসতে নৌকো। তার ওপর বর্ষার জলে ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের ভাসিয়ে দেওয়া ছোটো-বড়ো কাগজি নৌকো, কলার মোচা ও কলাগাছের বাকলের নৌকোর ছড়াছড়ি। বাড়ির উঠোনে খেলে যায় ছোটো ছোটো মাছ। সে-মাছ ধরার জন্যে ছোটোবেলায় সে কী মত্ততা! সন্ধে হতেই পাটখেতে ধানখেতে বঁড়শি পেতে রেখে আসার হিড়িক। ঘণ্টা দু-ঘণ্টা পর পর লণ্ঠন হাতে জল ঝাঁপিয়ে যেতে অনেক সময় হাসতে হাসতেই বঁড়শিতে সাপও তুলে নিয়ে এসেছে আমাদের মধ্যে অনেকে মাছের সঙ্গে সঙ্গে। সাপের ভয় ভয়ই নয় যেন! পুল থেকে দল বেঁধে লাফিয়ে পড়ে বর্ষার জলস্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়ার আনন্দও ভুলে যাওয়া চলে না। এমনি কত কী! শারদ বঙ্গের মাধুর্যও যেন ম্লান এখানে এক হিসেবে। মনে হয় বর্ষার বিক্রমপুরকে যারা দেখেনি, বিক্রমপুরের আসল রূপের সঙ্গেই তারা অপরিচিত।
আরও পরের কথা। আকাশে একটি-দুটি করে সবেমাত্র তারা ফুটতে শুরু করেছে। তারই ছায়া পড়েছে গোয়ালিনির কাকচক্ষু দিঘির জলে। কতকাল আগের কোন গোয়ালিনির স্মৃতি বয়ে চলেছে এ দিঘি জানা নেই। তবে সে অজানা গোয়ালিনির আভিজাত্য অস্বীকারেরও উপায় নেই। আমাদের বাড়ির সমুখ দিয়েই চলে গেছে বজ্রযোগিনী-মীরকাদিমের সড়ক। এই সড়কই আমাদের রাজপথ। রাজপথের ধারে অনেক দিঘির মতো গোয়ালিনি দিঘিরও একদিন মর্যাদা ছিল। কিন্তু আজ সে হৃত যৌবনা, তার কচুরিপানাময় জঞ্জাল রূপ আজ আর হয়তো কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। আমরা ছোটোবেলায় এ দিঘির ঘাটে বসে কত সময় কাটিয়েছি, কত গল্প করেছি, ছুরিতে কেটে, ঘেঁদা ঝিনুকে চেঁছে দিনের পর দিন খেয়েছি কত কড়া-কাঁচা আম! সে সবই আজ স্মৃতি।
দিঘির পাড়ের শ্মশানের আগুনের শিখাও চোখে ভাসে। কিন্তু আমার বাঙাল দেশজুড়ে আজ যে আগুন জ্বলছে তার লেলিহান শিখার, তার দাহিকা শক্তির প্রচন্ডতার বুঝি তুলনা নেই! সে-আগুনে ছাই হয়েছে মরা মানুষের অস্থি-মজ্জা-মেদ, এ আগুনে পূর্ণাহুতি তাজা তাজা হাজারো জীবন।
আমার গাঁয়ে পথচলতি মানুষ দলে দলে চলে উত্তরে দক্ষিণে–কাজ সেরে কেউ বাড়িমুখো, কেউ বাড়ি ছেড়ে কাজে, আবার কেউ বা হয়তো চলেছে আড্ডায়। রাত পড়তেই পথের এপাশে-ওপাশে কোনো-না-কোনো বাড়িতে নিশিকান্ত বা হরলালের কীর্তন আর না হয় শিশরির ‘ত্রিনাথের মেলা’-র গান শুরু হয়েছে বা হয়নি। এমনি ছিল আমার গাঁয়ের প্রায় প্রতিদিনকার সান্ধ্য পরিবেশ। সুখবাসপুরের সুধাকণ্ঠ গায়ক দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায় আমাদের বাড়িতে প্রায় রোজই শ্যামাসংগীতের আসর বসাতেন এবেলা-ওবেলা। আর আমার ভক্তপ্রবর ঠাকুরদা স্বর্গীয় রাজমোহন বসু মজুমদার কেঁদে বুক ভাসাতেন সেসব গান শুনে। ভক্তিরসের বাহুল্য দেখে সেই ছোটোবেলায় আমরা হয়তো অনেক সময়ই হেসেছি। কিন্তু দুর্গামোহনের,
মা আছেন আর আমি আছি,
ভাবনা কি আর আছে আমার?
মায়ের হাতে খাই পরি
মা নিয়েছেন আমার ভার।
এসব সুললিত গানের কথা আজও যে ভুলতে পারিনি! কর্মক্লান্ত দিনের অন্যান্য অবকাশে কলকাতার ফুটপাথে চলতে চলতে কতদিন এসব ছায়াছবির মতো ভেসে উঠেছে মনের পর্দায়।
আজও মনে ক্ষণে ক্ষণে জেগে ওঠে বিক্রমপুরের সেই গ্রাম, যে গ্রামের নাড়ির সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার নাড়ির যোগ। যখনই চিন্তায় হাতড়াই, কাছে এসে পড়ে বজ্রযোগিনী গ্রামের স্বপ্ন-মাখানো স্নেহভরা সেই স্মৃতি। মায়ের মতো ভালোবেসেছি এই গ্রামকে। আমার প্রায় সব-ভুলে-যাওয়া শৈশব আর সব মনে-থাকা কিশোর-জীবনের কান্না-হাসির দোলায় স্মৃতিতে অম্লান হয়ে আছে আমার সেই ছেড়ে আসা গ্রাম।
বাংলাদেশের ইতিহাসে বজ্রযোগিনীর নাম অবিস্মরণীয় সত্তা। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে ও ঐতিহ্যে এ গ্রাম লক্ষ গ্রামের দেশ বাংলায় যেকোনো একটি নয়, স্বমহিমায় এ সবিশেষ। সুদূর অতীতের অন্ধকার যুগে বাংলার সত্যসন্ধানী যে ছেলে একদিন জ্ঞানের আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে দূরধিগম্য হিমাচলের দুস্তর গিরিমালা অতিক্রম করে তুষারঘেরা ঘুমের দেশ তিব্বতে উপনীত হয়েছিলেন ভগবান তথাগতের বাণী নিয়ে, সেই জ্ঞান-তাপস দীপংকর শ্রীজ্ঞান অতীশের পুণ্য জন্মভূমি এই গ্রাম। কিন্তু আজ আর পুকুরপাড়ায় সেই দীপংকরের ভিটেয় সন্ধ্যাদীপ জ্বলে না লক্ষ জনের কল্যাণ কামনায়, চলার পথে আজ আর হয়তো কোনো মানুষ সে-মহামানবের অসীম করুণার প্রত্যাশায় মাথাও নোয়ায় না ভক্তিবিনম্রচিত্তে ‘নাস্তিক পন্ডিতের ভিটে’-র সমুখ দিয়ে যেতে যেতে।
পাশের ঐতিহাসিক গ্রাম সেন রাজাদের অধিষ্ঠানভূমি রামপাল আজ শ্রীহীন। তার ভগ্নাবশেষের স্কুপের তলায় আশপাশে অতীত স্মৃতির যেটুকু শুচিতা অবশিষ্ট ছিল তারও সবটাই হয়তো আজ বিনষ্ট। মাইল দীর্ঘ রামপালের সেই বল্লাল দিঘি। প্রজার জলকষ্টে দুঃখপীড়িতা রাজমাতা ছেলের কাছে জানিয়েছিলেন তাঁর মনের বেদনা। পরদিনই দিঘি খননের আদেশ হল। রাজমাতা প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যতদূর পথ পায়ে হেঁটে যেতে পারবেন ততদূর দীর্ঘ ও তার অর্ধেক প্রস্থ জলাশয় হবে, বল্লাল রাজার এই হল প্রতিশ্রুতি। প্রজার জলাভাব মোচনে পথ চলায় রাজমাতার বিরাম নেই। রাজ-পারিষদগণের চোখে-মুখে দেখা দেয় উদবেগের ছাপ। শেষটায় কি সারারাজ্য জলময় হয়ে যাবে! পায়ের সামনে অজ্ঞাতে আলতা ঢেলে দিয়ে কৌশলে তখন কে থামিয়ে দেয় রাজমাতাকে পুরো একমাইল পথ হাঁটার পর। রক্তচিহ্ন দেখে ভয়ে থমকে দাঁড়ান মা-রানি। মাইলব্যাপী দিঘির জন্ম হল রাতারাতি। সারারাজ্য মুখর হয়ে উঠল বল্লালরাজ ও রাজমাতার জয়ধ্বনিতে। কিন্তু আজ? আজ আর প্রজার দুঃখে রাজার মন কাঁদে না, এমনকী রাজমাতা, রানি বা রাজ-ভগিনীদেরও নয়। সেখানে আজকের রাজা প্রজারক্ষায় নয়, প্রজাহননে যেন উল্লসিত–রাজপুরুষেরা তারই নানা সাফাই গায় বেতারে, বক্তৃতায়! আজ আর জয়ধ্বনিতে নয়, ক্রন্দন আর্তনাদে সারারাজ্য মুখরিত।
বল্লালদিঘির উত্তর পাড়ের সুদীর্ঘ গজারি গাছ আজও সেন রাজার উদার উন্নত মনের সাক্ষ্য বহন করে দাঁড়িয়ে আছে কি না জানি না, তবে চার বছর আগেও জীর্ণ সে-গাছের ছায়াতলে দাঁড়িয়ে অনুভব করেছি প্রায় আটশো বছর আগের গৌরবময় অতীতকে। প্রচলিত ধারণা, রাজার হাতি বাঁধা থাকত এ গাছে। কিন্তু দৈবপ্রভাব ছাড়া শ-শ বছর ধরে কী করে একটা গাছ সগৌরবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, বিক্রমপুরের মানুষের মনে এ জিজ্ঞাসা অতিপুরাতন। ছেলে-মেয়ের দীর্ঘায়ুর আশায় কত মা এই অমর গাছের শীতল ছায়ায় বসে মানত করেছে, প্রার্থনা জানিয়েছে ভগবানের কাছে। কিন্তু আজকের ভগবানের দরজায় কি মানুষের কোনো প্রার্থনাই পৌঁছোয়? পূর্ববাংলায় আজ যাঁরা ক্ষমতার মালিক তাঁদের দম্ভকে স্বীকার করে আজও কি সেই গজারি গাছ তার অমরত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে?
রামপালের হরিশ্চন্দ্রের দিঘির আশ্চর্য কাহিনিও বিস্মৃত হওয়ার নয়। কতবার মাঘী পূর্ণিমার দিনে এ দিঘির অলৌকিক ব্যাপার দেখতে গিয়েছি বড়ো ঠাকুরদার সঙ্গে, আশপাশের গ্রাম থেকে এসেছে দলে দলে নর-নারী আর ছাত্র-শিক্ষকের দল। সারাবছর ধরে যে দিঘির জল থাকে মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে ‘দাম’-বনজংলায় ঢাকা, মাঘী পূর্ণিমায় তার সে কী সজল হাসিমাখানো রূপ! যে দামে’-র ওপর গোরু চরে, ছেলেরা ঘুড়ি ওড়ায়, পাখি ধরে, সাপ তাড়া করে দৌড়োয় দিনের পর দিন, সে ‘দাম’ এই একটি দিনের জন্যে দিঘির জলের কোন অতল তলায় তলিয়ে যায় কে জানে? পূর্ণিমা পেরিয়ে গেলে আবার ভেসে ওঠে যেমনি তেমনি। ব্রিটিশ সরকার এ বিস্ময়ের যবনিকা উত্তোলনের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে এ প্রাচীন কীর্তির অবমাননাকারীর দন্ড ঘোষণা করে নোটিশ টাঙিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু ‘হাকিম নড়লেও হুকুম নড়ে না, এ প্রবাদ হয়তো শুধু প্রবা দই। তা ছাড়া পুববাংলায় আজ হয়তো কোনো হুকুমেই পরোয়া নেই কারুর। মানুষের জীবনেরই কোনো মূল্য নেই যেখানে, সেখানে অজানা অতীতের হিন্দুকীর্তি রেহাই পাবে অমর্যাদার হাত থেকে এ আশা দুরাশা বই কী! তবু আশা হয়, ভেঙে গেছে যে স্বপ্ন, বাংলার বহ্নি-হৃদয়ে আবার উজ্জ্বল হয়ে আলো দেবে সেই স্বপ্ন।
কলকাতার মানুষ হয়ে গেছি আজ। কিন্তু জন্মেছিলাম যার আঁচলজড়ানো কোমল মাটির নরম ধুলোয় তাকে তো ভুলতে পারিনি। দুঃখ আছে মনে, দিন-রাত্রির খাটুনিতে অবসাদ নামে দেহে, আর্থিক দৈন্যও থেকেই যায়। তবু ছুটি পেলেই একছুটে চলে যেতে ইচ্ছে করে প্রায় তিন-শো মাইল দূরের সেই গ্রামে! বিক্রমপুরের স্বপ্ন-ছোঁয়া সেই শ্যামল গাঁয়ের পায়ে হাঁটা পথ দিয়ে চলতে চলতে ইচ্ছে করে ছেলেবেলার মতো আবার গলা ছেড়ে সুর ধরি : ‘সার্থক জনম মাগো জন্মেছি এই দেশে। এদেশ জন্মদুখিনী, তবু এই আমাদের সাত রাজার ধন, এক-শো হিরে-মানিক জ্বলে তার আকাশে।
কলকাতা থেকে গাড়ি করে গোয়ালন্দ। সেখান থেকে স্টিমারে পদ্মা পেরিয়ে ধলেশ্বরীর কোলে কমলাঘাট স্টেশন। স্টেশনের পর বন্দর। তারই অদূরে মীরকাদিমের হাট পেরিয়েই শুরু আমার গাঁয়ের রাস্তা, যাকে আগে বলেছি ‘রাজপথ’। খানিক এগিয়ে এলেই আমার গ্রামের মুখে সুখবাসপুরের সেই কড়ই গাছ। এখানে এসে বিশ্রাম-সাধ না জেগেছে এমন লোক বড়ো নেই। সেই কড়ই গাছের তলায় তিনসিঁড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কত দুপুর, কত রাতে প্রার্থনারত মুসলমানদের আজানের ডাক ভেসে এসেছে বাতাসে বাতাসে। মনে হয়েছে এ ডাক বন্ধুত্বের, মৈত্রীর, ভালোবাসার।
আর একটু যেতেই নিবারভাঙার পুল। আমাদের কত আড্ডা জমত সেখানে স্কুলপালানো, ঘরপালানো কৈশোরের ক্লান্তিহীন উল্লাসে। কৈশোরের সেই বাঁধন না-মানা উন্মাদনা নিয়ে গ্রামোন্নয়নের কাজে সেবাদল করেছি, ডন-কুস্তির আখড়া করেছি, আর সেইসবেরই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়েছিলাম শান্তিসুধা লাইব্রেরি। সেসব আজ দূর অতীতের গর্ভে। কিন্তু তা হলেও সে-অতীত একথাই প্রমাণ করে, গ্রামের ছেলেরা একজোট হয়ে কত ভালো কাজ করতে পারে। এসব কাজে আমরা পেয়েছিলাম জীবনদার সাহচর্য। সময়ে-অসময়ে কতদিন কতরকমে পালিয়ে পালিয়ে ছুটে গিয়েছি তাঁর কাছে, তাঁর কর্মকেন্দ্র মহকুমা-শহর মুনসিগঞ্জে। অগ্নিসাধক সেই জীবনদার কাছে দীক্ষা পেয়েছিলাম সেবার, দেশপ্রেমের, বিপ্লবের। আজ তাঁর সান্নিধ্য থেকে অনেক দূরে সরে থাকলেও মুক্তিপাগল শঙ্কাহরণ সেই জীবনদার অকপট আদর্শ-নিষ্ঠার কাছে আজও মাথা নোয়াই।
অসহযোগের যুগে কংগ্রেসনেতা সূর্য সোমের বক্তৃতা শুনেছি, বক্তৃতা শুনেছি নামজানা না জানা আরও অনেক দেশভক্তের। তখন আমি কতটুকু! কিন্তু জ্বলন্ত বিদ্রোহের যে আগুন তাঁরা জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন মনে, সে-বহ্নিদাহনে জীবনের সব জড়তা, হীনতা-দীনতা পুড়িয়ে ছাই করে খাঁটি মানুষ হওয়ার প্রেরণা পেয়েছিলাম সেদিন। অনেক চ্যুতি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও বড়ো হয়ে স্নেহ পেয়েছি তাঁদের অনেকের, বিশেষ করে সূর্য সোমমশাইয়ের। বছর বারো আগে শেষদেখা হয়েছিল সোম মশাইয়ের সঙ্গে। অবকাশ যাপনে কিংবা কোনো উপলক্ষ্যে গিয়েছিলেন তিনি দেশের বাড়িতে কর্মস্থল ময়মনসিংহ থেকে। আমিও তখন গ্রামে রয়েছি ছুটিতে। আমার কথা শুনেই খবর পাঠালেন। প্রণাম করতেই পিঠ চাপড়ে পাশে বসিয়ে বললেন, ‘শেষজীবনটা গাঁয়ের মাটিতেই কাটাব ঠিক করেছি। তোরাও আসিস, যখন ফুরসত পাবি ছুটে আসবি। গ্রামগুলোকে যদি বাঁচিয়ে রাখতে পারিস তো দেশ আপনি এগিয়ে যাবে। কথাগুলো সবই ঠিক। কিন্তু শেষজীবনটা গাঁয়ে কাটাবার শখ আর তাঁর মেটেনি। অল্পদিন পরেই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হয়েছে তাঁকে প্রকৃতির আহ্বানে। আজ যে পরিবেশ তাতে আমাদেরই কি আর গ্রামসেবার সে-সুযোগ ঘটবে?
বাংলাদেশের অন্যতম জনবহুল এই গ্রাম। উনিশ-কুড়ি হাজার লোকের বসতি। আঠাশটি তার পাড়া। তিন-তিনটে ডাকঘর আর তিনটে বাজারে সদা জমজমাট এই জনপদ। বছর কুড়ি-একুশ আগে বেশ একটা বড়ো হাসপাতালও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তিলতৈল-খ্যাত জি. ঘোষের অর্থে। কিন্তু অর্থ যারই হোক, রোগ চিকিৎসায় কোনো পার্থক্যই কখনো দেখিনি হিন্দু-মুসলমানে।
গ্রামের রাজধানী বলতে গুহপাড়া। বড়ো বাজার, বড়ো ডাকঘর, সাত-শো আট-শো পড়ুয়া ছেলের হাই স্কুল, খেলার মাঠ সব কিছুই এখানে। গ্রামের জমিদার গুহবাবুদেরই কীর্তি অধিকাংশ। জমিদারির প্রতাপ নিঃশেষিত হয়েছে রায়বাহাদুর রমেশচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে। পল্লি আভিজাত্যর ঐতিহ্য তাঁর মধ্যেও লক্ষ করেছি, কিন্তু তাঁর পরে আর নয়। দানে-অপচয়ে প্রায়-নিঃশেষ ভান্ডারও দোল-দুর্গোৎসব ও রথযাত্রার সমারোহে কোনো ব্যাঘাত ঘটাতে পারেনি। চৈত্রসংক্রান্তিতে বাবুর বাড়ির দরজা থেকে বাজার ও খেলার মাঠজুড়ে বসে ‘গলৈয়া’-র মেলা। অফুরান আনন্দের ঝড় বয়ে যায় ক-দিন ধরে এ উপলক্ষ্যে। চৈত্রমাসে নীলোৎসবে চড়কপুজো ও কালীকাছ’-এর নাচের কথা ভুলে যাওয়া বিক্রমপুরের কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। এই কালীকাছ’-এর নাচে ভট্টাচার্যপাড়ার দলই ছিল সবার সেরা। আর সত্যি নাচে-গানে এ পাড়ার নামই ছিল সবচেয়ে বেশি। সোমপাড়া-ভট্টাচার্যপাড়া ‘অ্যামেচার ড্রামাটিক ক্লাব’ও ছিল এ পাড়াতেই এবং এই নাট্যাভিনয় ক্লাবটি ছিল আমার গাঁয়ের একটি গৌরবের বিষয়।
শ্রাবণ মাস পড়তেই ধুম পড়ে যেত মনসার পাঁচালি গানের। মূল গাইয়ে ছিলেন স্বর্গীয় লালমোহন বসু মজুমদারমশাই। মনসার ভাসান গান সম্পর্কে তাঁর ছিল অদম্য উৎসাহ। তিনি নিজেই তিন খন্ডে এক পাঁচালি লিখে ফেলেছিলেন। আর সারা-শ্রাবণ মাস ধরে সে-পাঁচালির গানই গাওয়া হত। লালমোহন, হরিমোহনের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গান ধরতাম আমরা সব ছেলে-মেয়ের দল, পদ্মে গো পুরাও মনের বাসনা বলে। কীই-বা আমাদের এমন বাসনা ছিল? সাপের কামড় থেকে আত্মরক্ষার জন্যেই তো ছিল আমাদের আকুল আবেদন। দেশবিভাগের যে বিষ-যন্ত্রণা আমরা আজ মর্মে মর্মে অনুভব করছি তার তুলনায় সাপের কামড়ও যে নিতান্তই সামান্য!
পড়ার জীবনের অনেক স্মৃতিই আজ সামনে এসে ভিড় করে। মনে পড়ছে নাহাপাড়ায় হরিমোহন বসুর পাঠশালার আটচালার কথা। হাতেখড়ি হরিমোহনের কাছেই, তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। কতদিন পড়া ফাঁকি দিয়ে পাঠশালা পালাতাম দলবেঁধে ঘুড়ি ওড়াতে কি হাডু-ডু খেলার নেশায়। যখন আকাশ বেয়ে নামত বৃষ্টি আমাদেরও মনের দিগন্তে তখন সাদা মেঘের ভেলা ভাসিয়ে আসত ছুটির আমন্ত্রণ। হাই স্কুলের ছোটোখাটো মানুষ হেডমাস্টার অম্বিকাবাবুর চলন, চেহারা ও চাহনিতে অধ্যয়নার্থী ছাত্রদের জাগাত হৃৎস্পন্দন। তাঁর চলার পথে দু-শো হাতের মধ্যে যেতে সাহস হত না কারুর। আহা, কী ভালোই না বাসতেন তিনি ছাত্রদের। আদিনাথবাবু, তারাপ্রসন্নবাবু, পন্ডিতমশাই, বিরজাবাবু, এঁরা সবাই ছাত্রবন্ধু। স্নেহে ও শাসনে বাপ-মায়ের মতো আপন। অথচ দেশে গিয়ে এঁদের দেখা পাব এমন ভরসা কি আর আছে?
ধীরেনবাবু ইতিহাস পড়াতেন আমাদের। খুব ভালো লাগত তাঁর মুখে বাঙালির অতীত গৌরবের কথা শুনতে এবং বইয়ে পড়তেও। পরীক্ষার আগে ইতিহাসের বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়তাম। মধ্যরাত্রে দক্ষিণের বিলে নলখাগড়ার বন থেকে ভূতুমের ডাক শুনে জেগে উঠে আবার শুরু করতাম ধীরেনবাবুর ইতিহাসের পড়া। সেই ধীরেনবাবুই ছিলেন গত কয় বছর ধরে আমাদের জয়কালী হাই স্কুলের হেডমাস্টার। কিছুদিন আগেও শুনেছিলাম, সাহস করে তিনি তখনও আমাদের গ্রামেই আছেন। তাঁর সাহসিকতাকে নমস্কার জানিয়েছিলাম সে কথা শুনে। কিন্তু এ কী, তিনিই হঠাৎ একদিন আমার অফিসে এসে হাজির তাঁর দুঃখের কথা জানাবার জন্যে! তাঁর যে ছাত্র তাঁকে সপরিবারে মানে মানে সরে পড়ার পরামর্শ দিল, গ্রাম ছেড়ে চলে আসার পথে তারই সাঙ্গোপাঙ্গদের হাতে আটক পড়তে হল তাঁকে সদলবলে। প্রিয় ছাত্রের মধ্যস্থতায় শ-দুই টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে গুরুমশাই ছাড়া পেয়ে কোনোক্রমে পরিজনসহ পদ্মা পেরিয়ে কলকাতায় এলেন বটে, কিন্তু পাড়াগাঁয়ের সরল-মন শিক্ষকের বিস্ময় কাটল না–এ কী হল, কেমন করে হল, এসব প্রশ্ন ঘিরে রইল তাঁর মনকে। একলব্যের কাল অতলান্ত অতীতের গর্ভে, সে আর ফিরে আসবে না জানা কথা। তা হলেও সদ্য স্বাধীন পাকিস্তানে বাংলারই মাটিতে যে গুরুদক্ষিণা দেয় হবে গুরুমশাইয়ের আর ছাত্র হবে গ্রহীতা, এ ছিল অকল্পনীয়। তবু তাই হল এবং তাই পাকাপাকি নিয়ম হয়ে দাঁড়াবে কি নতুন শরিয়তি রাজত্বে, কে তা বলতে পারে? কৈশোর থেকে যৌবন, যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পা দিয়েছি। কলকাতায় এসে খবর পোঁছোল ভুখা বাংলার পঞ্চাশী মন্বন্তরের হিংস্র আক্রমণে বজ্রযোগিনী মুমূর্ষ। বুদ্বুদা, অমিয়দা প্রভৃতির সাহায্যে কলকাতায় বজ্রযোগিনী সমিতি গড়ে উঠল হীরালাল গাঙ্গুলি মশাইকে সভাপতি করে। অর্থ আর অন্নবস্ত্র সাহায্য সঙ্গে করে গ্রামের পথে পা বাড়ালাম।
তখন প্রায় সন্ধে। দিগন্ত ছোঁয়ানো আকাশে ম্লান মেঘের ছায়া। আকাল। আঠাশপাড়ার গ্রাম বজ্রযোগিনী কন্ঠাগতপ্রাণ। বকুলতলার ঘাটে স্নানার্থী জলার্থী মেয়েদের আর ছেলেদেরও ভিড় যেখানে জমে উঠত, সেখানেও বিরলতর হয়ে আসে সন্ধ্যাগুঞ্জন। সোমপাড়ার পুলে কত অক্লান্ত আড্ডা জমিয়ে পথচারীদের অতিষ্ঠ করে তুলেছে পাড়ার ছেলের দল। সে-বছর সেখানেও দুরন্তদের ভিড় নেই। সোমপাড়া আমার শৈশবের স্বপ্নভূমি।
মন্বন্তর সর্বভুক সরীসৃপের মতো গ্রাস করে নিচ্ছিল গ্রাম-হৃদয় বাংলার জীবন। মনের টানে আমাদের সামান্য প্রচেষ্টা নিয়ে সেদিন গিয়েছিলাম গ্রামে। খবর শুনে এলেন এক মাস্টারমশাই। বললেন, মনে রেখেছ বাবা গ্রামকে? গ্রাম যে যায়। আমরা শিক্ষক। আমাদের আর কী আছে, তোমরা ছাত্ররাই আমাদের যা-কিছু সম্পদ। আনন্দে যেন উচ্ছল হয়ে উঠলেন তিনি। আমার স্কুলজীবনের উত্তর-তিরিশের আধা-প্রৌঢ় গুরুমশাইয়ের চোখে-মুখে বার্ধক্যের নামাবলি। সবগুলো চুল গেছে পেকে। সময় যে নিঃশব্দ চরণে এগিয়ে চলেছে এ তারই স্বাক্ষর।
তারপর চলে গেল আরও কত বছর। নাড়ির টানে বার বার ছুটে গিয়েছি গ্রামে। তার মায়ের মতো স্নেহস্পর্শে অবুঝ হয়ে উঠেছে মন। দূর গ্রামের মুসলমানদের এক মেয়ে, ডাকতাম তাকে মধুপিসি বলে। কেউ নাকি ছিল না তার। প্রায়ই আসত আমাদের বাড়ি। আমরাই তার সব, একথা যে কতবার সে আমাদের বলেছে তার লেখাজোখা নেই। কোনোদিন মনে হয়নি মধুপিসি মুসলমান। নিজের বাড়ির এটা-ওটা, মাঠের ফল-মূল-শাক প্রায়ই সে নিয়ে আসত আমাদের জন্যে। আগ্রহে পরমানন্দে মধুপিসির দেওয়া সেসব জিনিস গ্রহণ করতাম।
শুধু কি এই? একদল বিহারি দেহাতি মানুষ–প্রতিবছর পুববাংলার পল্লিতে পল্লিতে যারা এসে সাময়িক আস্তানা গাড়ে, তার একটা বড়ো অংশ একরকম পাকাপাকিভাবেই রয়ে গিয়েছিল এই গ্রামে; আমাদের গ্রামের মানুষই হয়ে গিয়েছিল তারা–আমাদের সঙ্গে একাত্মা। তারা ডুলি-পালকি বইত, অনেকে এমনি আর সব কাজকর্মে রুটি জোগাত নিজেদের। অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট রায়বাহাদুরের বাঁধা পালকি ছিল একটা। তাঁর চারজন বেহারাও ছিল নির্দিষ্ট। তারাই ছিল গ্রামের বিহারিদের মোড়ল। আজও কি তারা আমার গ্রামে আছে?
আমার সোনার গ্রাম! সিদ্ধা যোগিনী বরদার নাম-মহিমায় মহিমান্বিত এ গ্রাম। সংস্কৃত শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র ছিল এক সময় এ জনপদ। গোবিন্দ বেদাধ্যায়ী, প্রসন্ন তর্করত্ন, শশিভূষণ স্মৃতিরত্ন, শ্রীনাথ শিরোমণি ও দ্বারিকানাথ তর্কভূষণ প্রমুখ ভারত-খ্যাত পন্ডিতেরা এ গ্রামেরই সন্তান। আমার গাঁয়েরই নাহাপাড়ায় জন্মেছিলেন লোককবি আনন্দচন্দ্র মিত্র। আনন্দচন্দ্রের হেলেনাকাব্য, মিত্ৰকাব্য, বিবিধ সংগীত প্রভৃতি রচনা বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বড়ো দুঃখেই কবি গেয়েছিলেন–
(এসব) দেখে শুনে এ দুর্দিনে বল মা তারা, যাই কোথা?
মিলে যত ভন্ড ষন্ড দেশটা করলে লন্ডভন্ড;
ধর্মকর্ম থোকার টাটি, (যত) বদমায়েসির ফাঁদ পাতা!
… … … … …
না জানি কি কপাল দোষে হতভাগ্য বঙ্গদেশে
পশুর বেশে অসুর সৃষ্টি কল্লে দারুণ বিধাতা!
দেশ হয়েছে আস্ত নরক! একদিনেতে এসে মড়ক,
গো-বসন্তে উজাড় করলে তবে যায় মনের ব্যথা!!
প্রায় এক-শো বছর আগের বাংলাদেশের অবস্থায় যে কবির কোমল প্রাণে দেখা দিয়েছিল এমনি মর্মপীড়া, আজকের হতভাগ্য বাঙালির অবস্থা দেখতে হলে কী করে তা সহ্য করতেন কবি, তা কি আমরা কল্পনাও করতে পারি?
‘জাতের নামে বজ্জাতি’ যারা করে, তীব্র কশাঘাতে তাদের সংশোধনের কত চেষ্টাই না করেছেন চারণ-সম্রাট মুকুন্দ দাস! তাঁর যাত্রাগানের কথা বাঙালি কি ভুলতে পারে কোনোদিন? ছোটোবেলায় আমাদের গাঁয়েই শুনেছি তাঁর কত পালাগান। বাঙালির অধঃপতনে তাঁরও খেদের অন্ত নেই। তিনিও গেয়েছেন–
মানুষ নাই দেশে
সকল মেকি সকল ফাঁকি, যে যার মজে আপন রসে।
আর তারই প্রতিফল আমরা আজ ভোগ করছি হাতে হাতে। চারণ-সম্রাট আজ আর বেঁচে নেই, তাঁর জন্মগ্রাম বিক্রমপুরের বানারিও কীর্তিনাশা পদ্মার গর্ভে। তার জন্যে দুঃখ করার আর কী আছে! সারা পুববাংলা ছাড়াই তো আমরা। রাজা রাজবল্লভের রাজনগর আর চাঁদ রায়-কেদার রায়ের রাজবাড়ি গ্রাস করেই তো পদ্মা নাম নিয়েছে কীর্তিনাশা পদ্মার কবল থেকে রক্ষা পেলেও পাকিস্তানের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার তো উপায় ছিল না। আজ তাই তো ভাবি, আমার গ্রাম যে থেকেও নেই। সে না-থাকার ব্যথা যে আরও দুঃসহ!।
যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সারাভারতের মুক্তির সাধনায় সর্বত্যাগী, তাঁর পিতৃপুরুষের বাসভূমি আমার গাঁয়ের অদূরবর্তী তেলিরবাগ গ্রাম স্বাধীন ভারতের অন্তর্ভুক্ত নয়–সে পুণ্যক্ষেত্র আজ বিদেশে, বিদেশির শাসনাধিকারে, এ ভাবতেও শরীর শিউরে ওঠে। কিন্তু কী হবে ভেবে?
কে জানত এমনি করে ছেড়ে আসতে হবে গ্রামকে। শরণার্থী পরিজন পরিবেশে এই মহানগরীর এক প্রান্তে সংকোচে আজ দিন কাটাই। তবু আশা জাগে, আজ যে দেশ দূর, দুঃশাসনের হাত থেকে সে-দেশকে, সোনার বাংলার হৃৎপিন্ড সে-বিক্রমপুরকে একদিন ফিরে পাব আমার মনের কাছে।
.
সাভার
প্রতি অঙ্গে সে-গাঁয়ের স্পর্শ। বড়ো মিঠে. বড়ো মধুর। হাঁটি হাঁটি পা পা করে ওখানেই তো চলতে শিখেছি। ওরই হিজলতলায়, পদ্মবিলে, ধলেশ্বরীর উচ্ছল স্রোতে সারাশৈশবটা কেটেছে। বুধু পন্ডিতের পাঠশালা, বুড়ো বটের দিঘল জটা কত স্মৃতির মাধুর্যেই না মধুময়!
ময়ূরপঙ্খির গল্প শুনতে কতদিনই না বসেছি ধলেশ্বরীর ধারে। সন্ধে নেমেছে। চাঁদ উঠেছে কালো গাঁয়ের মাথায়। শত মুক্তোর প্রাচুর্য নিয়ে মাতাল হয়েছে ধলেশ্বরী। এক চাঁদ শত চাঁদ হয়ে আছড়ে পড়েছে ঢেউয়ের দোলায়। চেয়ে রয়েছি, কেবল চেয়ে থেকেছি।
সন্ধের ঝিরঝিরে হাওয়ায় নোঙর খুলে পাল তুলেছে মাঝিমাল্লারা। তাদের কলকন্ঠে খিলখিল করে হেসে উঠেছে যেন জ্যোৎস্নাস্নাত নিবিড় আকাশ। দিগন্ত তুলেছে প্রতিধ্বনি। কিশোর মন সন্ধান করেছে মধুমতীর দেশের, ওই বাঁক পেরিয়ে মাঠ ছাড়িয়ে।
কেষ্ট বৈরাগীকে ভুলতে পারি? কত ভোরেই না ঘুম ভেঙেছে তার সুললিত গানের সুরে। মায়ের আঁচল ধরে কতদিনই না বাইরে এসে দাঁড়িয়েছি। ভোরের হাওয়া আমার সর্বাঙ্গ বুলিয়ে গেছে মায়ের স্নেহের মতো। আমার আঁখির আবেদনে আবার নতুন করে গান ধরেছে কেষ্ট,
সখিগো…ওগো প্রাণসখি! এই করিয়ে তোমরা সকলে, না পুড়াইয়ো রাধা অঙ্গ না ভাসাইয়ো জলে, মরিলে বান্ধিয়া রেইখো তমালেরি ডালে…গো।
বিরহিণীর অশ্রুভেজা এ অন্তিম আবেদনে কৈশোরের অবুঝ মনও কেঁদে উঠেছে। কেষ্ট বৈরাগীর মরমি সুর ধলেশ্বরীর পলিমাটির মতোই নরম।
এমনি কত টুকরো টুকরো স্মৃতি আর স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা আমার গ্রাম সাভার, ঢাকা জেলার একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। বুকে তার কত শতাব্দীর অক্ষয় ইতিহাস, অতীত সভ্যতার বিলীয়মান কঙ্কাল। এখানে রাজ্য ছিল, রাজা ছিল একদিন, ছিল শিক্ষা আর সংস্কৃতির প্রাণবান প্রবাহ। এ দেশের বাণী সেদিন পৌঁছোত দূরদূরান্তে…হিমালয়ের শিখরচূড়া পেরিয়ে। দীপংকরের জ্ঞানের প্রদীপ এখানেই প্রথম জ্বলেছিল–গুরুগৃহে তাঁর শিক্ষা শুরু হয়েছিল এখানে। সেদিনের সাভার ছিল সর্বেশ্বর নগরী, রাজা হরিশ্চন্দ্র পালের রাজধানী, সর্ব-ঐশ্বর্যে মন্ডিত। বৌদ্ধধর্মের বন্যা নেমেছিল এর দিকে দিকে। ধর্মরাজিকা কত বিহার মাথা তুলেছিল এ অঞ্চল ঘিরে। কত ভক্তমনের অন্দরমহলে ঠাঁই করে নিয়েছিল সর্বেশ্বর নগরী…আমার সাভার।
সেদিনের স্মৃতি আজও নিঃশেষ হয়নি। বাজাসনে’ আজ রাজার আসন না থাকলেও সে গৌরবময় দিনের কত স্বপ্ন-কথা এর মাটির অঙ্কে অঙ্কিত রয়েছে। সেদিনের কত অস্পষ্ট স্বাক্ষর দিকে দিকে আজও বর্তমান। কর্ণপাড়ার ভগ্নস্তূপ, ‘বাজাসন’ রাজপ্রাসাদের শেষচিহ্ন কোটবাড়ি আজও তো পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
আমরাও কি আর কম ঘুরেছি? কতদিন, কত কাঠফাটা রোদ্দুরে বাড়ি থেকে পালিয়েছি দল বেঁধে। একটা নতুন কিছু যেন আবিষ্কারের ইচ্ছে। দুধসাগর, নিরেমিষ, লালদিঘি এমনি কত পুকুরের ধারে ধারেই না সারাটাবেলা কেটেছে। রবীন্দ্রনাথের সেই খ্যাপার মতো আমরা যেন করে ফিরেছি সেই পরশমণির অনুসন্ধান। আমগাছের ছায়ায় বসে বসে ডাক দিয়েছি রমজানকে, আজমত শেখকে। বাজাসনের এখানে-ওখানে আজ ওদেরই উপনিবেশ। দুধে ধোয়া সাদা-বাবরি নেড়ে রমজান বলেছে কত গল্প, কত পুকুরের ইতিবৃত্ত; ‘নিরামিষ্যিতে মাছ থাহে না কর্তা, ওডা রাজার মা’র পুকৈর।–অবাক হয়েছি। বোবার মতো চেয়ে রয়েছি রমজানের দিকে। কোদাল ধোয়ার ইতিহাস বলেছে রমজান, কোটরাগত চোখ দুটো টেনে টেনে। ওটাই নাকি রাজা হরিশের শেষ পুকুর। শত পুকুর শেষ করে ওখানেই নাকি কর্মীরা কোদাল ধুয়ে উঠেছিল–রমজান তার নানার কাছে থেকে শুনেছে সেসব কথা। সেদিন রমজানের কোনো কথাই অবিশ্বাস করিনি। সাভারের এপাশে-ওপাশে ছড়িয়ে থাকা শত শত পুকুর দেখে বুড়ো রমজানের কথা সত্যি বলেই মনে হয়েছে।
আজ আরও কত কথাই না মনে পড়ে। স্মৃতির মণিকোঠায় বিগত দিনের কত ছবিই না। জ্বলজ্বল করে ওঠে। যখন ভাবি, কিশোরবেলার স্বপ্ন-ছাওয়া সে গ্রামখানি থেকে কত দূরে সরে এসেছি, যখন মনে হয় দেশবিভাগের পাপে আত্মার আত্মীয় সে-গাঁখানি আমার আজকে বুঝি পর হয়ে গেল, তখন সজল চোখের আরশি দু-খানি কত বিচিত্রতর ছবিতেই না ভরে ওঠে! গত দিনের কত কথা ও কাহিনি মনের দোরে এসে বারে বারে ঘা মেরে যায়।
মনে পড়ে নববর্ষের কথা। বৈশাখের রুদ্রদূত নতুনের জয়পত্র নিয়ে আসে। সারাগাঁয়ে পড়ে যায় সাড়া। দোকানিদের দোকানগুলো ফুলেপাতায় সেজেগুজে নতুনকে জানায় অভ্যর্থনা। গাঁয়ের মেঠোপথ মুখর হয়ে ওঠে আনন্দপাগল ছেলে-ছোকরাদের কলকন্ঠে। অপূর্ব হয়ে ওঠে সারা গাঁখানি! অপূর্ব মনে হয় জীবনের স্বাদ।
বিকেলের দিকে মেলা বসে। পাঠানবাড়ির বটের ছায়ায়। নমপাড়ার হীরু সর্দার, বক্তারপুরের জনব আলিরা শুরু করে ছড়ি খেলা। আগ্রহাকুল দর্শকেরা ভিড় করে থাকে চারপাশে। প্রতি বছর প্রতি বৈশাখের প্রথম দিনটি এমনি কত সর্দারের ছড়ির প্যাঁচেই না হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত! বিজয়ীর সর্বাঙ্গে কতজনেরই না উৎসুক দৃষ্টি পিছলে পড়ে!
হীরু সর্দারের নাম আছে। ঝাঁকড়া চুলে ঝাঁকুনি মেরে সে যখন ছড়ি নিয়ে দাঁড়ায় তখন তাকে নতুন মানুষ বলে মনে হয়। দিঘল দুটি চোখ থেকে ঠিকরে পড়ে আগুনে দৃষ্টি। নিশ্বাসের তালে তালে বুকের পাটাও যেন ফুলে ফুলে ওঠে। হেই…হেই…সামাল..সামাল..শব্দ করে তিড়িং করে লাফ দিয়ে ওঠে হীরু সর্দার। পায়ের তলায় মাটি যেন একেবারে কেঁপে ওঠে। উৎসুক জনতার অজস্র করতালির ভেতর খেলা শেষ করে কোমরের গামছা খুলে হীরু বাতাস করতে থাকে। গাঁয়ের মেয়েরা আড়চোখে দেখে যায়।
বর্ষা নেমে আসে। শাওনের ঢল নামে গাঙে। নবযৌবনা ধলেশ্বরী আপন গরবে ফুলে ওঠে। ওপারের কাশবন ডুবে যায়। মজেযাওয়া খালগুলো ছল ছল করে ছোটে; চাষিপাড়ার এক একটি কুটিরকে এক-একটি দ্বীপের মতো দেখায়।
শাওনের অঝোরঝরা রাতের একটি ছবি মনে জেগে ওঠে। গাঙিনীর জলে হেলেদুলে একটি ভেলা ভেসে চলেছে। তালীবন শেষ হল। সমুখে শুধু জল আর জল। বেহুলার অকম্পিত বুক। মা কাঁদছে, ভাই কাঁদছে, কাঁদছে প্রতিবেশীরা। আর বেহুলার সংকল্পে পরিবর্তন নেই!
মনসা পুজোর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িয়ে আছে এই বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনি। পল্লিকবি জিইয়ে রেখেছেন চাঁদবেনের কথা। ভাসান গানের সুরে সুরে বেহুলার অবাধ অশ্রু আজও উছলে ওঠে। সনকার অশ্রুজলে কত সন্ধ্যায় কত মায়ের বুকও ভিজে যায়।
এ অঞ্চলে বহুল প্রচলিত এই গান। রাতের পর রাত গান চলে। বেহুলা-লখিন্দরের প্রথম পরিচয় থেকে বিদ্রোহী চাঁদের অন্তিম পরাজয় পর্যন্ত। হিন্দু-মুসলমান সমান শরিক সে-গানের। মাখন দাঁ, এমনকী কেদার মুনশিও। বেহুলার অটল সংকল্পে ভাই-এর ব্যথা যখন মূর্ত হয়ে ওঠে এ গানে,
না যাইয়ো না যাইয়ো বইন
শুন লো মোর মানা;
তুমি গেলে বইন লো আমার
মায় যে বাঁচব না।
তখন কতদিন লুঙ্গির কোণে ছাবেদালী ব্যাপারীকে চোখের জল মুছতে দেখেছি। হিদুর ‘কেচ্ছা’ সেদিনও মুসলমানের ‘গুণাহ’ বলে বিবেচিত হয়নি। সনকার অশ্রুর আড়ালে তারা যেন তাদের ব্যক্তিক দুঃখেরই ছবি দেখতে পেয়েছে।
শরতের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। এই সময়টির জন্যে সারাবছর ধরে কী বিপুল প্রতীক্ষা! সে কী আয়োজন! প্রবাসীরা ঘরে ফিরছে। ধলেশ্বরীর কূলে রোজই এসে নতুন নতুন নৌকো লাগছে। আমরা ছেলেরা গিয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়েছি। ক-দিনের জন্যে গাঙখালি লোকে ভরপুর। সবার সঙ্গে আবার নতুন করে পরিচয়।
হিন্দুপ্রধান গ্রাম সাভার। পুজো এখানে বেশ কয়েকখানিই হয়। তার মধ্যে দক্ষিণ ও উত্তর পাড়ার বারোয়ারি দুটি প্রধান। আগে উভয়ের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা হত, প্রতিমা তৈরি থেকে আরম্ভ করে গান-বাজনা নিয়েও। দক্ষিণীরা ঢাকা থেকে কারিগর আনালে, উত্তরেরা বিক্রমপুর পর্যন্ত ছুটত। দক্ষিণীরা তিন রাত গানের ব্যবস্থা করলে, উত্তরেরা নট্ট কোম্পানির যাত্রদলের সঙ্গে পাঁচ রাতের চুক্তি করে বসত। সন্ধে থেকে শুরু করে সারারাত চলত গান। এপাড়া হরিশ্চন্দ্র’ বই নির্বাচন করলে ওপাড়ায় আরম্ভ হয়ে যেত রামচন্দ্র।
ছোটোবেলায় দেখেছি দুর্গা পুজোর মুসলমানের আনন্দ কম নয়। হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের ঘরেও আসত নতুন কাপড়। মুসলমান মেয়েরা পাড়ায় পাড়ায় প্রতিমা দেখে বেড়াত। রং বেরঙের লুঙ্গি পরে গলায় গামছা ঝুলিয়ে এগাঁয়ের সেগাঁয়ের মুসলমানেরা সকাল সকাল ঠাঁই করে নিত যাত্রার আসরে। রামচন্দ্র’ কিংবা হরিশ্চন্দ্র’ পালায় হিন্দুর সঙ্গে তারা সমান ভাবেই হেসেছে ও কেঁদেছে। পূর্ববাংলায় দুর্গাপুজো ঠিক এমনি করেই হয়ে উঠেছিল সর্বজনীন উৎসব।
কোকিল-ডাকা বসন্তে আর একটি উৎসবে এ অঞ্চল মেতে উঠত। এটা যেন সত্যিকারের গণউৎসব। এতে চাষিদেরই উৎসাহ বেশি। ষাট বছরের বুড়ো পাঁচু মন্ডল হলুদবরণ কাপড় পরে পা দুটিতে ঘুঙুর বেঁধে দুলে দুলে নাচতেও লজ্জা করেনি। সারাবছরের দৈন্যেভরা জীবনকে ভুলে তারা যেন কেবল মুঠো মুঠো আনন্দ কুড়িয়েছে।
শিব পুজো বা শিব খাটনাও সাধারণ মানুষের উৎসব। এ অঞ্চলে এর প্রাধান্য কম নয়। অন্তত দশ-বিশ দল তো প্রতিবছরই আমাদের বাড়িতে এসে হাজির হয়েছে। শিব ঠাকুরকে মাথায় নিয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করেছে এরা। গলায় কয়েকখানি ‘মেডেল’ ঝোলানো ঢাকি হরকেষ্টার ঢাকের তালে তালে বুড়ো-কাঁচায় সমান হয়ে নেচেছে। নাচনার শেষে গান ধরেছে প্রেমানন্দ। উমার গান, নিমাই-সন্ন্যাসের গান। ডান হাতে মাথাটি রেখে প্রেমানন্দ যখন গেয়েছে,
সন্ন্যাসী হইয়ো রে নিমাই
বৈরাগী না হইয়ো,
(ওরে) ঘরে বইসে কৃষ্ণ নামটি
মায়েরে শুনাইয়ো।
তখন মায়ের চোখ দুটি কোন সে ব্যথার অনুভূতিতে যেন টলটল করে উঠেছে।
দিনে ‘খাটনা’, রাতে ‘কাছ’। ‘কাছ’ কথাটি এসময় সম্পূর্ণ এক নতুন অর্থে ব্যবহৃত হয়। নানাপ্রকার রঙ্গরসের ভেতর দিয়ে কাছ’ নাচের পরিসমাপ্তি ঘটে। এ যেন বাংলার আদিম নৃত্য। জনসাধারণের কাছে অসীম এর আবেদন। ছেলেবেলায় মায়ের বকুনি খেয়ে সারারাত্রি জেগে বাড়ি বাড়ি এ ‘কাছ’ দেখে ফিরেছি। মহাদেবঠাকুর যদি তার দীর্ঘ ত্রিশূলটি হাতে নিয়ে দু-একটি কথা বলেছে, তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করেছি। হিংসুটে রাধাবল্লভটা অনুতাপে জ্বলে জ্বলে মরেছে। সে-আনন্দ, সে-অনুভূতি আজও উপলব্ধিতে জাগে। ‘মুখা কাছ’ দুর্লভ শীল আজও মনের নিভৃতে অগোচরে উঁকি দিয়ে যায়। তাদের কি ভুলতে পারি?
কত মধুরই না ছিল সে সন্ধেগুলো। তাল-তমালের ফাঁকে ফাঁকে প্রদীপ জ্বলত, শাঁখ বাজত, কর্মক্লান্ত দিনের শেষে সারা-গাঁ-জুড়ে নেমে আসত একটা নিবিড় প্রশান্তির ছায়া। দোকানি ফিরত হাট থেকে, মাঠ থেকে ফিরত রাখালেরা। সন্ধের আঁধারে তলিয়ে যেত সকল বিচ্ছিন্নতা। নীরব নিথর গ্রামখানি দাঁড়িয়ে থাকত পূজারিনির মতো, একক–একনিষ্ঠ।
যেদিন চাঁদ উঠত আকাশে, সেদিনের আর এক ছবি। ফুলকেয়ারির ফাঁকে ফাঁকে শুরু হত আলো-আঁধারের খেলা। জুই ফুলের গন্ধে বাতাস হত মদির, স্বপ্নময় হয়ে উঠত আমার গাঁখানি।
মেয়েমহলে সেদিন যেন মহোৎসব। সকাল সকাল সান্ধ্য আয়োজন শেষ করে দুর্গাখুড়োর পাকা উঠানে সবাই এসে ভিড় করত। প্রিয়দার বউ আসত কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে, মেরুর মা আসত হাতের চেটোয় ‘সাদা’ গুঁড়ো নিয়ে। এমনকী ফুলী আর সুধী বোন, যারা সূর্যসাক্ষী করে পরস্পরের মুখদর্শন পর্যন্ত বন্ধ করেছিল, তারাও এসে পাশাপাশি মুখ ফিরিয়ে বসে থাকত। হায় রে! সে-নিবিড়তা, সে-মাখামাখি চিরকালের মতোই কি শেষ হল?
মতি সাধুকে ভুলব না। কীর্তনীয়া মতি সাধু। সারাতল্লাটে বিদেশে তার নামডাক। অমন মধুর কণ্ঠ, অমন ভাবানুভূতির তুলনা খুঁজে পাইনে–আজও যেন মনে লেগে আছে। অমন প্রাণ দিয়ে গান গাওয়া আর কি শুনতে পাব?
গোপাল আখড়া, হরি আখড়া, বড় আখড়া। গাঁয়ের এক-একটি কেন্দ্র এ আখড়া গুলোতে কতদিন মতির গান শুনেছি। জলকেলি, মাথুর প্রভৃতি পালা! হাতে চামর নিয়ে হেলেদুলে গান করেছে মতি সাধু। গলায় ঝোলানো গাঁদা ফুলের মালা এদিক-ওদিক গড়িয়ে পড়েছে। মাথুর পালায় গান ধরেছে সে এই বলে,
সর্ব অঙ্গ খেয়ো রে কাক
না রাখিয়ো বাকি,
কৃষ্ণ দরশন লাগি
রেখো দুটি আঁখি।
দোহারিরা সুর ধরেছে, তাল রেখেছে। তন্ময় হয়ে মতি সাধু শুরু করেছে কথকতা: ওরে কাক, ওরে তমাল-ডালে বসে থাকা কাক! তুমি আমার সর্বাঙ্গ নষ্ট করো। কিন্তু যে কৃষ্ণের বিরহ-ব্যথায় আমি জ্বলে জ্বলে পুড়ে পুড়ে মরছি, সেই নিঠুর কৃষ্ণের দর্শন-অভিলাষী আমার এই আঁখিযুগল কেবল তোমার কাছে ভিক্ষে চাইছি। এ দুটো তুমি বাকি রেখো।
কথকতার পর আবার সুর ধরেছে মতি সাধু,
বাকি রাখিয়ো,
কৃষ্ণ দরশন লাগি
বাকি রাখিয়ো।
খোল বেজেছে। মাথা নেচেছে। তালে তালে পড়েছে করতালি। কিন্তু মনের অজান্তে। আঁখিপল্লব দুটি কখন যে একেবারে ভিজে উঠেছে–কেউ হয়তো টেরও পায়নি।
বাংলা লোকসংস্কৃতির এক বিশিষ্ট অবদান এই কীর্তনগান–শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে পল্লির গৃহকোণে বেজে চলেছে এর সুর, এর আবেদন। বাংলার সাধারণ মানুষের উপলব্ধিতেও এ গান সাড়া জাগিয়েছে। কেবলমাত্র রাধাকৃষ্ণের কথা নয়, রামমঙ্গল, নিমাই সন্ন্যাস, এমনি আরও কত গানের মাধ্যমেই না পল্লির জনমানস রস সংগ্রহ করেছে। কত দিন, কত সন্ধ্যায় এরই আবেদনে কুসীদজীবী অধর ঘোষকেও কৈবর্তপাড়ার ভোলানাথের সঙ্গে কোলাকুলি, গলাগলি করতে দেখেছি। হিসেবি মানুষ অখিল সাহাও কেঁদে কেঁদে বুক ভাসিয়েছে।
সে-গ্রাম আজ কত দূরে! পদ্মা-মেঘনা পেরিয়ে কোথায় সে ধলেশ্বরী! এত স্মৃতি, এত স্বপ্ন-রঙিন সে-মোহন পরিবেশ থেকে আজ আমি নির্বাসিত। দেশবিভাগের পাপে আমার মতো ছিন্নমূল আরও অনেকে দিগবিদিকে ছড়িয়ে গেছে। ভেঙেছে সমাজ, ভেঙেছে ঘর সংসার। শান্ত সুনিবিড় আমার সে-গাঁখানি আজ বুঝি নির্বাক হয়ে গেছে। পুঁটি পিসিরা কোথায়? অমন অনাবিল স্নেহের উৎসটি আজ কত দূরে! কাজ না-থাকা অলস দুপুরবেলা আজ তো আর কেউ তেমন দরদ দিয়ে ডাকে না, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে আজ তো আর কেউ কাছে এসে বসে না। আজ আমি যেন আকাশ থেকে ছিটকেপড়া তারা–স্মৃতির জ্বালায় তিল তিল করে পুড়ে মরছি।
নিশ্চয়ই আমাদের তুলসীতলাটি আজ একেবারে নির্জন। আজ আর সেখানে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলে না, কাঁসর-ঘণ্টা বাজে না, সদিবোনের রাধাকৃষ্ণের গানে সান্ধ্য হাওয়াও আর তো সজল হয়ে ওঠে না! পূর্ববাংলার নিভৃতে থাকা আমার সে-গাঁখানি রাতের আঁধারে আজ বুঝি কেবল থমথম-ই করতে থাকে!
ধলেশ্বরী তেমন করেই বয়ে যায় কি? কাশফুলগুলো আজও কি তেমন করেই ফোটে? জ্যোৎস্নাস্নাত বালুচরে রাখালিয়া বাঁশি আজও কি তেমন করেই বেজে ওঠে? গভীর রাতে ঘুম ভেঙে এমনি কত প্রশ্নই না মনে জাগে! চোখের সামনে ভিড় করে আসে ছবির পর ছবি। ব্রহ্মচারীর মাঠ, রজনি সা’র মশান–আরও কত কিছুর কথাই না মনে পড়ে যায়! স্মৃতির জ্বালায় আঁখিপল্লব দুটি বারে বারে ভিজে ওঠে। মনে হয় সে যেন হারিয়ে গেছে। যে ছিল প্রিয়, যে ছিল শ্রেয়, সে যেন আর আমার নয়। আমার স্বপ্নে-থাকা মাটির মাকে মা বলে ডাকবার অধিকারও যেন আজ আমি হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু তার আহ্বানের তো শেষ নেই! আজও যেন সে আমায় ঠিক আগের মতোই ডাকে। স্বপ্ন-শিয়রে ধলেশ্বরী আজও যেন আছড়ে পড়ে হাতছানি দিয়ে ডেকে বলে বার বার–আয়, আয়, ওরে আয়!
.
ধামরাই
আবর্তিত হয়ে চলেছে মহাকালের রথচক্র। সেই রথচক্রের আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রথিত হয়ে আছে মানুষের জীবন। এমনি এক মহাকালের ত্রিকালবিধৃত বিগ্রহরূপের সঙ্গে শৈশবেই পরিচিত হয়েছিলাম আমাদের গ্রামে। ধামরাই-এর মাধব ঠাকুরের রথের সেই ঘূর্ণমান চক্র দেখে মহাকালের চিরপ্রবহমান গতিস্রোতের যে বিশাল ব্যাপ্তি উপলব্ধি করেছিলাম ছোটোবেলায়, সে-স্মৃতি আজও অবিস্মরণীয়। প্রথম দৃষ্টি মেলেই যে গ্রামের মাটির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, যার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে শৈশব ও যৌবনের দিনগুলো অতিবাহিত করেছিলাম, এক অভাবনীয় ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সে-জন্মভূমি গ্রাম-জননীর মাটি থেকে ছিন্ন হয়ে দূরান্তরের এই জনারণ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেললেও সেদিনের স্মৃতি আজও আমার লক্ষ্যহীন যাযাবর জীবনের ধূলিধূসর মুহূর্তগুলোকে আশার আলোকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। সে-গ্রাম যে আমার জননী।
বংশাই নদীর এক তীরে ধু-ধু করছে প্রান্তর–যতদূর দৃষ্টি যায়, শ্যামল সবুজ। ধান্যশীর্ষগুলো দু-হাত বাড়িয়ে আকাশের দিকে কীসের প্রত্যাশী যেন–মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যায় বাতাসে দুলে দুলে শোঁ শোঁ শব্দে কেন যেন বাঁশি বাজায় ওরা। এপারে মল্লিকঘাটের সামনে ঠক-ঠক হাতুড়ি পেটানোর শব্দ-বড়ো বড়ো মালবাহী নৌকো তৈরি চলছে সেখানে। ঘাট থেকে একটি রাস্তা এঁকে-বেঁকে কিছুদূর গিয়ে দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে–একটি গিয়ে মিশেছে বাজারে যাওয়ার সড়কে, আর একটি চলে গেছে তাঁতিপাড়ার দিকে। দ্বিতীয় পথটি ধরে কিছুদূর গেলেই পাঁচিল-ঘেরা বাগান, পেছন দিকে মস্তবড়ো পাকা দোতলা বাড়ি। এ রাস্তার ওপরেই বাড়ির খিড়কি-দোর। সদর দোর বড়ো সড়ক থেকে পুবদিকে বেরিয়ে-আসা একটা গলির ওপর। তামাম দুনিয়ায় এইটেই ছিল আমার মাথা গোঁজবার ঠাঁই। জীবনের এতটা বয়েস এখানেই কেটেছে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে। কোনোদিন দু-মুঠো অন্নের জন্যে কপালে চিন্তার রেখা ঘনিয়ে ওঠেনি। অতিথি এসেছে, কখনো সেবার ত্রুটি হয়নি। আজ আমরাই অতিথি হয়ে পরের অনুগ্রহপ্রার্থী। অদৃষ্টের এ নির্মম পরিহাস!
আমাদের গ্রামটি ছিল প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। চাষি, জেলে, গোয়ালা, কামার, কুমার, ছুতোর, তাঁতি, ডাক্তার, কবরেজ প্রভৃতি নানারকমের লোকের বসবাস ছিল সেখানে। নিত্যপ্রয়োজনীয় কোনো সামগ্রীর অভাব সেখানে হত না। প্রত্যহ বসত বাজার। সপ্তাহে সোমবার ও শুক্রবার হাট। অত বড়ো হাট এদিকটায় ছিল বিরল। নদীপথে ও উন্নত ধরনের গ্রাম্যপথে দূরদূরান্তের পল্লিগুলোর সঙ্গে সংযোগ ছিল তার, তাই ধামরাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল এ অঞ্চলের একটি বড়ো ব্যবসাকেন্দ্র। শিল্পের মধ্যে তাঁত ও কাঁসার জিনিসপত্রই ছিল প্রধান। শিল্পে-ব্যাবসায়ে সমৃদ্ধ এমন গ্রাম এ অঞ্চলে খুব কমই দেখা যেত।
১৯৪৬ সালে বাংলার বুকে যখন সহসা সাম্প্রদায়িক দাবানল জ্বলে উঠল, রাজধানী থেকে সুদূর শান্তিময় পল্লিতেও যখন তার লেলিহান শিখা বিস্তৃত হল এবং তারই প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র বাংলার বক্ষ দীর্ণ খন্ডিত হয়ে গেল-ধামরাই শ্মশানে রূপান্তরিত হতে চলেছে তখন থেকেই। গ্রামের শেষে কয়েকখানি ঘর মুসলমানদের। তাদের সকলেই প্রায় কৃষক। প্রতিবেশী হিন্দুর সঙ্গে মিলেমিশে চাষ-আবাদ করে এবং হিন্দু জমিদার-মহাজনের সাহায্য নিয়ে বেশ শান্তিতেই কাটছিল তাদের দিন। তাই বাইরের উসকানি তাদের খুব একটা উৎসাহিত করতে পারেনি। তবু দুর্গের মতো এই হিন্দুপ্রধান গ্রামের আকাশেও দেখা দিল অন্ধকারের অনিশ্চিত আশঙ্কা। পথ চলার সময় আপন ছায়াও সচকিত করে তুলতে লাগল আমার গাঁয়ের মানুষকে।
ত্রস্ত জীবন ও লাঞ্ছনা-গ্লানির অন্ধকূপ থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে বিদেশে গিয়ে সংসার পাতবার সুযোগ ও সংস্থান যাদের ছিল কিংবা অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে নতুন ভাগ্য রচনা করার দুর্জয় দুঃসাহসিক মনোবল যাদের ছিল–তারা যতটা সম্ভব বিষয় আশয় বেচে দিয়ে বহুপুরুষের বুকের রক্তেগড়া আবাসভূমিকে প্রণাম করে অশ্রুজলে বিদায় নিল। আপন কর্মশক্তি দ্বারা নতুন কর্মক্ষেত্রে নিজেকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় শ্রমজীবীদের আছে তারাই গেল সর্বপ্রথম। ধনিক ব্যাবসায়ীরাও ব্যাবসা গুটিয়ে স্থানান্তরে যাওয়ার জন্যে উদ্যোগী হলেন। বিত্তবান জমিদারেরা সরিয়ে নিয়ে গেলেন তাঁদের অস্থাবর সম্পদ। ডাক্তারেরাও চলে গেলেন, শহরের ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি না করে গ্রামের দিকে গেলে কোনোরকমে চলে যাবে, এই ধারণা। পড়ে রইল কৃষক-জেলে ও হতভাগ্য মধ্যবিত্তরা! কৃষক-জেলে জানে, গতর খাটালে কোথাও ভাতের অভাব হয় না। তবু শেষপর্যন্ত দেখে যাবে। কিন্তু মধ্যবিত্তরা কোথায় যাবে?–কোন ভরসায়? যাদের বাগানের শাকসবজি, পুকুরের মাছ আর কিছু ধানি-জমির ধান ও তার আয়ের ওপর দিন চলে– তাদের কী উপায়? ডিঙি নিয়ে নদীতে বা পুকুরে জাল ফেলতে তারা জানে না, গোরু নিয়ে মাঠে লাঙল ঠেলতে পারে না, মাথায় মোট বয়ে উপার্জনও কল্পনার অতীত। যদি সকল সম্পত্তি উচিত মূল্যে বেচা এবং পশ্চিমবাংলায় উচিত মূল্যে অনুরূপ সম্পত্তি কেনা সম্ভব হত, তবেই সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যেত। কিন্তু উচিত মূল্যে বেচাও হবে না, কেনাও হবে না। কেনা-বেচার কালোবাজারের দাঁড়িপাল্লার দৌরাত্মে সকল সম্পত্তি উজাড় হয়ে যাবে। মধ্যবিত্ত ক্ষুদ্র ব্যাবসায়ীদের অবস্থা তেমনি। সবচেয়ে মর্মান্তিক অবস্থা শিক্ষক ও বেসরকারি চাকুরেদের। নিঃস্ব রিক্ত অবস্থায় এসে পশ্চিমবাংলার দ্বারে দ্বারে আশ্রয় ও জীবিকার সকরুণ আবেদন জানিয়ে মাথা কুটে মরবে তারা। হতভাগ্যদের নাম পুনর্বসতির দফতরে ও এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের পর্বতপ্রমাণ ফাইলের তলায় চাপা পড়ে পড়ে কখন জঞ্জালের ঝুড়িতে স্থান পাবে। এদের ভরসা সরকারের অনুগ্রহ। কিন্তু অদৃষ্টের দোষে প্রায় সবার অবস্থাই যে আমারই মতো দাঁড়াবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ কাউকেই যে আর বিশ্বাস করা যায় না এ সংসারে, কারও কথার ওপরেই যে নির্ভর করা চলে না!
আমার কথাই বলি! পরকে বিশ্বাস করে নিজেকেই যে বিপন্ন করেছি বারে বারে। যারা না জানে এপারে এসে তারাও তো সেই বিপদের পথেই পা বাড়াবে। বাইরের সহানুভূতি দেখে মানুষের অন্তর চেনা যায় না। এ অভিজ্ঞতা অনেক বাস্তুহারা পরিবারেরই হয়েছে কলকাতার শেয়ালদা স্টেশনে, পশ্চিম বাংলার নানা শরণার্থী শিবিরে। এমনি এক শিবির দেখতে এসে মনে পড়ে সেই কবে ধামরাইয়ে আমাদেরই এক প্রতিবেশীর দক্ষিণের ঘরের দাওয়ায় বসে এক বাউল গেয়েছিল তার একতারা বাজিয়ে,
মনের মানুষ না পেলে সেই মনের কথা কইব না;
মনের মানুষ পাবার আশে
ভ্রমণ করি দেশ বিদেশে
মানুষ মিলে শত শত মন তো মিলে না–
প্রাণ সজনি গো!
সংসারী মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে সংসার-বিবাগি বাউল আরও গেয়েছে,
শিমুল ফুলের রং দেখে ভাই রঙ্গে মেত না;
ও ভাই দেখলে চেয়ে মনের চোখে,
অহরহ পড়বে চোখে
চোরের নায়ে সাউধের নিশানা–
প্রাণ সজনি গো!
কিন্তু কলকাতায় নবাগত আমার গাঁয়ের সর্বহারা সরল-মন মানুষদের কি সে ক্ষমতা সে মনের অবস্থা আছে শিমুল-শিউলি বেছে নেওয়ার! কাজেই পুববাংলার সাধারণ মানুষের কাছে এ স্বাধীনতার স্বাভাবিক দান–-প্রতারণা থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোনো উপায়ই যে দেখছি না আমি।
কলকাতায় এসেছি আত্মরক্ষার পথের সন্ধানে। এই জনকোলাহলের মধ্যে দাঁড়িয়ে মনে পড়ে, আমাদের ধামরাইয়েও তো দূরদূরান্ত থেকে সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী আসত মাধব-দর্শনে। মেলা বসত। মাধবঠাকুরের ঘাট থেকে যাত্রাবাড়ি পর্যন্ত অসংখ্য বিপণি। কতরকম খেলনা, হাঁড়ি-পাতিল, ধামা-কুলো, বাক্স-ট্রাঙ্ক, বাসনপত্র, ছবি-ফোটো, মাটির ঠাকুর প্রভৃতির বিরাট সমাবেশ। কতরকম খাবারের দোকান ও রেস্টুরেন্ট। ম্যাজিক শো, সার্কাস। যাত্রীদের ভিড়ে গ্রামে তিলধারণের স্থান থাকত না। ঠাকুরমন্ডপে, দালানে, প্রতিটি গৃহের বারান্দায়, গাছের তলায়–সর্বত্র যাত্রীদল। সঙ্গে মেলার সওদা। মুড়ি, মুড়কি, ঢেপের খই, বিনি খই, চিনির মট, তিলা-কদমি, তেলেভাজা, দই-জিলিপি দিয়ে তাদের চলছে ফলার ভোজন। তা ছাড়া নুনবিহীন খিচুড়ি প্রসাদ কেনারও ধুম পড়ে যেত বিকেল বেলা। অসংখ্য বিপণির অপূর্ব শোভায়, আলোকসজ্জায়, ম্যাজিক-সার্কাসের ড্রাম-পেটানোর আওয়াজে, যাত্রীদের কোলাহলে, শিশুদের ভেঁপুর শব্দে সমস্ত গ্রামখানা উৎসবমুখর–সর্বত্র উৎসাহ-উদ্দীপনা, মুক্ত প্রাণের আনন্দ-উচ্ছ্বাস। কিন্তু কলকাতার এই হট্টগোলে আনন্দের পরিচয় কতটুকু?
ধামরাইয়ের মাধবঠাকুরের রথ সুবিখ্যাত। অত বড়ো রথ বোধ করি বাংলাদেশে আর কোথাও নেই। পাঁচতলা উঁচু। বত্রিশটি লোহার বেড়-দেওয়া চাকা। ওপরে ওঠবার চওড়া সিঁড়ি। সম্পূর্ণ কাঠের তৈরি রথটি। পৌরাণিক চিত্র খোদাই ও সুন্দর ভাস্কর্যশিল্পে অনন্য। রথটি রাখা হত গ্রামের মাঝখানে সুবিস্তৃত সড়কের ওপর। গ্রামের বাইরে থেকেও দেখা যেত তার চূড়া। দূর থেকে মনে হত যেন একটি মন্দির। নবাগতদের কাছে ছিল এক বিস্ময়। লক্ষাধিক লোকের সমাগম হত রথ-টানা উপলক্ষে। মেলাও বসত তিন সপ্তাহ ধরে। অপূর্ব দ্রব্যসম্ভার, অতুলনীয় ছিল তার আয়োজন। রথ চলত বিশ হাজার বলিষ্ঠ হাতের যুক্ত টানে। সে-দৃশ্য সত্যই দর্শনীয়। কিন্তু আজ?
দেশবিভাগের পর পাক-নাথের রক্তচক্ষুর দাপটে জগন্নাথের রথ আর এক পা-ও অগ্রসর হয়নি। মেলা-উৎসব শরিয়তি শাসনের ভয়ে অনির্দিষ্ট কালের জন্যে আত্মগোপন করেছে। যাত্রীদল সারাগ্রামে ভিড় জমিয়ে তুলে তাদের নিদ্রার ব্যাঘাত করতে আর সাহসী হয়নি।
তীর্থক্ষেত্ৰ ধামরাই। সুপ্রাচীনকালে সংস্কৃত নাম ছিল ‘ধর্মরাজিকা। তারপর পালি নাম ধম্মরাই থেকে আমরা পেয়েছিলাম আমাদের আধুনিক গ্রাম ধামরাইকে। বাস্তবিকই ধর্মপাগল ছিল আমার গাঁয়ের লোকগুলো। কিন্তু এত ধর্ম-সাধনার এ কী সিদ্ধি?–ধামরাইয়ের মানুষ হল ধামছাড়া! রথ, মাঘী পূর্ণিমা, উত্থান একাদশী ও চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষ্যে চিরকাল সেখানে তীর্থের উল্লাস মূর্ত হয়ে উঠত। আর এখন? এখনও সেসব উৎসবের দিন ঘুরে ঘুরে প্রতিবছরই আসে, কিন্তু তারা যেন একে একে এসে স্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে অতিসন্তর্পণে পালিয়ে যায়।
অতীতের স্মৃতি-তরঙ্গ ভেসে চলেছে দূরে, আরও দূরে, মহাকালের মহাসমুদ্রে। এপারে পুনর্বাসনের প্রার্থনা নিয়ে আমরা যারা ঘুরে বেড়াই এক-একটা পর্বদিন তাদের হৃদয়দোরে নিয়ে আসে অতীত স্বপ্নের দুঃসহ আঘাত। কিন্তু ধ্বনির যেমন প্রতিধ্বনি আছে, আঘাতেরও তো তেমনি আছে প্রত্যাঘাত। এপারে যে প্রতিনিয়ত আঘাত আসছে আমাদের বুকে, তার প্রত্যাঘাত কবে পৌঁছোবে ওপারে?
সাত সাতটি পুরোনো দেবালয়ের আশিসপূত ধামরাই। সর্বক্ষণ সরগরম থাকত সারাগ্রাম। সকাল-সন্ধ্যায় দেবালয়ে দেবালয়ে শঙ্খ-ঘণ্টার আরতি-বাজনায় ও উলুধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠত সমগ্র পল্লি। পূর্ববাংলার শান্ত পল্লি-সন্ধ্যা আজ কি কাঁসর-ঘণ্টার বাজনায় তেমনি চঞ্চল হয়ে ওঠবার সুযোগ পায়? সেদিনও শুনেছি, আমার গাঁয়ের দেবালয়ে এখনও নাকি পূজারতি চলে, কিন্তু নীরবে! বাজনা নিষিদ্ধ না হলেও ভয়ের কারণ, তাই বাজনা বন্ধ। প্রহরে প্রহরে শেয়াল ডাকে, ঝিল্লিরব ওঠে–কিন্তু কীর্তনগান আর শোনা যায় না। অথচ এই কীর্তনগান ছিল মাধব-ক্ষেত্র ধামরাই গ্রামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শ্রীমাধবের কৃপার ওপর ভরসা করে আজও যেসব কীর্তনীয়া পড়ে আছে গ্রাম-মায়ের মাটির বুকে তাদের কণ্ঠ আজ রুদ্ধ। সমস্ত ভয়ভীতি ও নিযেধাজ্ঞার বাঁধ ভেঙে কবে সেই রুদ্ধকণ্ঠ আবার নামকীর্তনে মেতে উঠবে কে জানে?
এখনও বংশাই নদীর তীরে প্রতিদিন প্রভাত আসে, সন্ধ্যা নামে। কিন্তু সে-প্রভাত, সে সন্ধ্যার স্নেহ-পরশ তো আর আমার অনুভব করার অবকাশ নেই। বংশাইয়ের বুকে নৌকো পাড়ি দিয়ে মাটির মাকে ছেড়ে এসেছি, বিদায় দিয়ে এসেছি তাঁকে চোখের জলে–আসতে বাধ্য হয়েছি। আমার মতো আরও অসংখ্য মানুষ শরণার্থীর বেশে এসে আশ্রয় নিয়েছে এই সীমান্তে। তারা জানে না কী তাদের পাপ, কী তাদের অপরাধ। তারাও তো ভালোবাসত তাদের দেশকে, দেশের মাটিকে আর সবারই মতো। দেশ-জননী কেন তাদের তার কোল থেকে ঠেলে ফেলে দিল? আবার কি মা ডেকে নেবে তার এসব নিরপরাধ সন্তানদের?
বাল্য ও কৈশোর-জীবনের কথা মনে আসে অহরহ আর অন্তরখানি ডুকরে কেঁদে ওঠে। ভোজনবিলাসী বাঙালদেশি মানুষ আমরা। খেতে-খাওয়াতে সমান আনন্দ পেত যারা, তারা আজ দু-মুঠো ভাতের জন্যে ঘুরে বেড়ায় দৈন্যের বিষণ্ণতা নিয়ে। অথচ খাওয়া বাঁচিয়ে বাঁচবার কথা পুর্ববাংলার মানুষ কোনোদিন ভাবতে পারেনি। কবিগুরু আমাদের লক্ষ করেই হয়তো রহস্য করে লিখেছিলেন,
খাওয়া বাঁচায়ে বাঙালিদের বাঁচিতে হলে ঝোঁক
এদেশে তবে ধরিত না তো লোক!
অপরিপাকে মরণ ভয়
গৌরজনে করিছে জয়
তাদের লাগি কোরো না কেহ শোক।
কিন্তু রাজনীতির পাপচক্রে আমাদের না খাইয়ে মারার যে ব্যবস্থা হয়েছে তার জন্যে শোক বা দুঃখ করার লোকও তো আজ বড়ো একটা দেখতে পাই না স্বাধীন দেশ এ ভারতবর্ষে!
আঁচলে ঘেরি কোমর বাঁধে,
ঘণ্ট আর হেঁচকি রাঁধো–
পূর্ববাংলার বাস্তুহারা মা-বোনদের শিবির-জীবনে এ দৃশ্য কি সম্ভব?
মনে পড়ে ছোটোবেলার আরও অনেক কথা। একবার পাঠশালা পালিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছিলাম বড়দার হাতে। দুষ্টু ছেলের সঙ্গে মিশতে দেখে তিনি যে আমায় শুধু গালমন্দই করেছিলেন তা নয়, কয়েক ঘা চাবুকও পড়েছিল আমার পিঠে। বুড়ো চাষি কদম আলি পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, বাজার ফিরতি তার নিঃশেষিত সবজির ঝাঁকা মাথায় নিয়ে। বড়দার হাতে আমার লাঞ্ছনা দেখে ব্যথায় যেন ভেঙে পড়ল কদম আলি। মাথার ঝাঁকাটি নামিয়ে রেখে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল বড়দার দু-হাত আর বলল মিনতি করে—’আর মাইরেন না দাদাবাবু, ছাইড়া দেন। আহা, হা! বেতের মাইরে খোকাবাবুর পিঠ ফাটাইয়া দিছেন এক্কেবারে! আর না, দোহাই আপনের, এইবারের মতন ছাইড়া দেন।’ কদম আলির সকরুণ আবেদনে বড়দা সেদিন সাড়া না দিয়ে পারেননি। সেবারের মতো সত্যি তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন আমায়। তবে বড়দার কঠোর শাসনের চেয়ে কদম আলির স্নেহস্পৰ্শই কিন্তু চিরকালের জন্যে গভীর দাগ কেটেছে আমার মনের মণিকোঠায়। সেই কদম আলিরা গেল কোথায়? গাঁয়ের মাটিকে প্রণাম করে আমরা যখন চলে এলাম, কই, কোনো মুসলমান ভাই তো সজল চোখে এগিয়ে এল না ‘যেতে নাহি দিব’ বলে! অসীম দুঃখে কদম আলির আত্মা হয়তো ডুকরে কেঁদে উঠছে– ফেলছে দীর্ঘনিশ্বাস আকাশ থেকে। কিন্তু সে দীর্ঘনিশ্বাসের তীব্র তরঙ্গস্রোত ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারবে কি মানুষের সমস্ত অশুভবুদ্ধি সোনার বাংলার বুক থেকে?
বেদে-বেদেনিরা প্রায়ই আসত আমাদের গাঁয়ে সাপের খেলা দেখাতে। বেহুলা-লখিন্দরের পৌরাণিক কাহিনি সুরে সুরে ছড়িয়ে দিয়ে তারা ঘুরে বেড়াত সাপখেলা দেখিয়ে। মন্ত্রমুগ্ধ হিংস্র সাপের সঙ্গে মানুষের মিত্ৰতা–তার সঙ্গে রহস্য ও রঙ্গরস সেসময় লক্ষ করেছি স্তব্ধ বিস্ময়ে। কিন্তু তখন তো বুঝতে পারিনি যে, মানুষ যদি কখনো সাম্প্রদায়িকতার বিষপানে সাপের মতো হিংস্র হয়ে ওঠে তার প্রতিবেশীকে আঘাত হানতে, তার জীবন-মান বিপন্ন করে তুলতে, তাহলে কোনো মন্ত্রেই আর তাকে বশীভূত করা সম্ভব হয় না।
শ্রীমাধবের ধাম ধামরাই মগ্ন আজ রাত্রির তপস্যায়। বংশাইয়ের কালো জলে আরও যেন কালি ঢেলে দিয়েছে রাত্রির অন্ধকার। যতদূর চোখ যায় শুধু অন্ধকার। কে জানে, কোথায় তার শেষ? এ প্রশ্ন আজ লক্ষ লোকের মনে। কিন্তু কে দেবে তার উত্তর?
.
খেরুপাড়া
ভারতবর্ষের বিশাল ভূমিখন্ডে বিদেশি বণিক-শাসনের অন্তিম লগ্নে মর্মান্তিক অভিনয় হল– ব্যবচ্ছেদের ছুরির ইঙ্গিতে ওরা হত্যার খঙ্গকে আহ্বান জানিয়ে খুশিমনে সরে পড়ল। মানুষের হৃদয়হীন দুর্বুদ্ধি সাপের ফণার চেয়েও সাংঘাতিক, তারই একটি দংশনে সমগ্র দেশ বিষ-জর্জর!
পদ্মা, মেঘনা, কর্ণফুলির তীরে তীরে সেই খঙ্গেরই বিদ্যুৎ-ঝিলিক দেখতে পাচ্ছি। মাটি রক্তে লাল, আকাশ লাল অন্তরের আক্রোশে, বাতাস-ভেজা চোখের জলের বাষ্পে–আর এই জল ঝরেছে অসহায় শিশু, বিপন্ন নারী, হাত-পা বাঁধা অক্ষম পুরুষের চোখ থেকে। ভাইয়ের মতো একান্ত আপন, একান্ত বিশ্বাসী যে, অন্ধকারে সে শ্বাপদের মতো লুকিয়ে এসে জ্বালিয়ে দিল ওর ঘর–ওর মাঠের ধান, গোয়ালের গোরু, ঘরের ঐশ্বর্য দস্যুর মতো লুঠ করে নিয়ে গেল চোখের সমুখ দিয়ে।
পূর্ববাংলার গ্রাম, গঞ্জ, জনপদ আজ নির্বাক, নিষ্প্রাণ। কল্পান্তের বিভীষিকায় চেতনা লুপ্ত তার। বারোমাসে তেরো পার্বণ যে দেশে, সেখানে সন্ধ্যার অন্ধকারকে চিহ্নিত করে আজ একটিও শঙ্খধ্বনি ওঠে না, বৃহস্পতিবারের লক্ষ্মী-সন্ধ্যায় গৃহবধূর আড়ষ্ট কণ্ঠ চিরে ফোটে না উলুধ্বনি। বোষ্টমের আখড়ার একতারা স্তব্ধ, গোপী-যন্ত্রের ছেঁড়া তারে হয়তো মরচে ধরেছে, হরিসভার ভক্তদের খোলের চামড়া কেটে দুরে আর আরশোলা তারমধ্যে এতদিনে সংসার ফেঁদে তুলেছে বুঝি বা!
লক্ষ-গ্রামশোভিত বাংলার এক গ্রামে, তার ধুলো-মাটির আদর-ভরা কোলে বিধি-নির্ধারিত একটি দিনে আমি প্রথম চোখ মেলে তাকিয়েছিলাম। দেশের ইতিহাসে সে-গ্রাম গর্বে-গৌরবে উজ্জ্বল নয়, কিন্তু আমার কাছে চিরস্মরণীয়, চিরবরণীয়–সে যে আমার মা, স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী। সেই মা আজ লাঞ্ছনায় অহল্যাজননীর মতো পাষাণ হয়ে আছে। আমরা পলাতক, তবু জন্মান্তরের প্রতীক্ষায় দিন গণনা চলে তার। পরিত্রাতার আবির্ভাব কি হবে না, তার রাত্রির তপস্যা কি সূর্যালোকের আশীর্বাদে ধন্য হবে না কোনোদিন?
কত গল্প, কাহিনি, স্মৃতি, উপকথায় জড়ানো আমার সেই মাটির মা–তার বুকজুড়ে আজ নির্জন শ্মশানের স্তব্ধতা! ভাবতেও চোখের কোণ জ্বালা করে জল ছুটে আসে। ঘরের কোলে সেই যে একফালি উঠোন, গণিতের মাপে বিশ-পঁচিশ গজের বেশি প্রশস্ত হবে না হয়তো অথচ সাতসমুদ্র তেরো নদীর চেয়েও তা দুস্তর দুরতিক্রম্য মনে হত, পার হতে গেলে পা ওঠে না–প্রাণ আর মানের দায়ে তাও শেষপর্যন্ত ছেড়ে এলাম, চোখের জলে তার শেষ ছবি এঁকে নিয়ে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে মনে, শাণিত বিদেশি ছুরির দাগের রক্তাক্ত সীমান্তরেখার ওপারে, যে বাড়ি যে ঘর পড়ে রইল, এখানে অদৃষ্টে নগর-লক্ষ্মীর অকুণ্ঠ দাক্ষিণ্য লাভ যদি ঘটেও, তবু কি আমার মন থেকে মুছে যাবে তার স্মৃতি? লাটসাহেবের বাড়ির নেমন্তন্ন কিংবা মোটা মাইনের সরকারি চাকরির গৌরবে কি আমি কোনোদিন ভুলতে পারব আমার জননী জন্মভূমিকে? যত দূরেই থাকি, মাইল-ক্রোশের হিসেব-কষা ব্যবধান যতই দীর্ঘ হোক-না কেন, সারাদিনের ব্যস্ততার পর অনেক রাত্রে আলো-নেবানো ঘরের অন্ধকারে বিছানায় যখন আমি একা, তখন সেই দূরান্তে ফেলে-আসা তাল, তমাল, হিজল, জিউল, নারকেল, খেজুর গাছের ছায়ায় ঘোমটা-টানা সেই স্নেহময়ীর জলভরা বিষণ্ণ দৃষ্টির ছায়া মনের ওপর এসে পড়ে। মধ্যরাত্রের মন্থর বাতাসে জড়িয়ে জড়িয়ে ভেসে আসে তার কান্না-করুণ কান্নার সুরে সে যেন আমায় ডাকতে থাকে, টানতে থাকে। চোখের পাতা থেকে কখন ঘুম ঝরে যায়। শিয়রের কাছের খোলা জানলা-পথে বিনিদ্র চোখে উত্তর আকাশে তাকাতে নজর পড়ে, সপ্তর্ষির দৃষ্টির আগুনে কী একটা জ্বলন্ত প্রশ্ন রাত্রির অন্ধকারকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দিচ্ছে। ও যেন আমার মনেরই প্রশ্ন, ঘোর অন্ধকারে আকাশের পটে গৃহপুঞ্জের জ্যোতিতে লেখা।
কলকাতার নগর-বেষ্টনী ছাড়িয়ে প্রায় দু-শো মাইল দূর। শেয়ালদা থেকে আট-দশ ঘণ্টার ট্রেনযাত্রার পর, গোয়ালন্দ থেকে স্টিমারে পদ্মা পার হয়ে ছোট্ট একটা স্টেশন-কাঞ্চনপুর। শালকাঠের তিনখানা তক্তা-ফেলা সিঁড়ি বেয়ে স্টিমার থেকে নেমে বালুর চরে পা দিতেই কী এক আশ্চর্য আনন্দে মনটা কলরব করে উঠত। দেশের আকাশ-আলো-মাটির স্নেহ সমস্ত শরীরে অনুভব করতাম। শিক্ষিত-নিরক্ষর, ভদ্র-অভদ্র পল্লিবাসীর সহজ সৌজন্যসূচক প্রশ্ন আন্তরিকতায় মাখা। অদ্ভুত ছেলেমানুষি খুশিতে বার বার মনে হত, দেশে এলাম তবে, এবার কিছুদিনের জন্যে শহরের গিলটিকরা নকল জীবনের বাইরে অনাবৃত আরামের ছুটি!
গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে ইছামতী–আমার শৈশবের বিস্ময়, কৈশোরের খেলার সঙ্গী। এর পারে দাঁড়িয়ে দূরের আবছা ধু-ধু বাঁকটায় নজর করতে করতে আমার প্রথম বিপুল পৃথিবীর স্বপ্ন দেখা, এর ওপর দিয়েই গেন্দু ভাইয়ের নৌকোয় চেপে প্রথম আমার কলকাতার উদ্দেশ্যে কাঞ্চনপুর স্টেশনে যাওয়া। ইছামতীর আঁকা-বাঁকা পথ। ছোটো ছোটো বাঁক। শীর্ণ শান্ত নদী, সংযত উচ্ছ্বাসহীন। বর্ষায় কূলে কূলে ভরে ওঠে জল, অথচ কূল ছাপিয়ে যায় না। জোয়ারের জলে তীব্র স্রোত–স্থানীয় লোকে বলে ‘ধার। কিন্তু পাড় ভেঙে ধারালো জিহ্বা বিস্তার করে সে ফসলের খেতের দিকে অগ্রসর হয়ে যায় না, আক্রমণ করে না নিঃস্ব চাষির জীর্ণ কুটির। সে যে এই গাঁয়েরই মেয়ে–মেয়ের মতোই সুখের চেয়ে দুঃখ বোঝে বেশি। গ্রীষ্মে জল শুকিয়ে খরখরে বালি বেরিয়ে পড়ে, কর্দমাক্ত ডাঙা জেগে ওঠে, এদিক-ওদিক। তার ওপরে পলিমাটির স্বাদে নিবিড় হয়ে গজিয়ে উঠে বনতুলসী, কালকাসুন্দি, শেয়ালকাঁটার ঝাড়-কচুরিপানার বেগুনি ফুলে চারদিক আলো হয়ে থাকে। পঙ্কিল জলের ওপর নৌকোর গলুই গলা উঁচু করে রাখে, তার চুড়োয় বসে কচ্ছপ-শিশু রোদে ঝিমোয়। জলের ধারে ধারে ঘোরে বক, বাবলা গাছের ডালে ধ্যানী মাছরাঙার নিঃশব্দ প্রহরগুলো কেটে যায়, পানকৌড়ি সেই পঙ্কিল জলেই অনবরত ডুব খেয়ে চলে।
লেখাপড়ার তাগিদে শহরে আসতে হয়েছিল। স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকেছি, স্বাভাবিক নিয়মে বয়স বেড়েছে। কিন্তু সেই যে অভ্যেস ছুটি হলেই পড়িমরি করে বাড়িতে ছোটা, তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। প্রবাস-জীবনের দিনগুলোর যাত্রাপথ বরাবর আমার টেবিলের সামনের দেয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারের পাতায় চিহ্নিত হয়ে থাকত–প্রতিদিন রাত্রে পড়াশোনা শেষ করে শুতে যাওয়ার আগে সেদিনের তারিখটা আমি কেটে দিতাম। বিছানায় শুয়ে মনে হত, একটা দিন তো কমল, বাড়ি যাওয়ার সময়টা স্পষ্ট পদক্ষেপে চব্বিশ ঘণ্টা সরে এল কাছে। স্কুলে যখন উঁচু মানের ছাত্র, জনৈক সহপাঠী একদিন শ্লেষ করে বলেছিল, ‘ছুটি হলেই বাড়ি ছুটিস, শহর ছেড়ে ভালো লাগে তোর পাড়াগাঁয়ে? কী আছে সেখানে সেই তো বাঁশবন, মশা, ম্যালেরিয়া, ঘেঁটু ফুল আর কানা কুয়ো।
রাগে ব্ৰহ্মর জ্বলে গিয়েছিল, ক্ষোভে দুঃখে জল এসে পড়েছিল চোখে। সেদিন বোকার মতো চুপ করে চলে এসেছিলাম; এত বড়ো মূর্খ প্রশ্নের জবাব দিতে পারিনি। পরে ভেবে দেখেছি, সব জিনিস সকলের বুদ্ধি দিয়ে মাপা চলে না। শান্ত ইছামতাঁকে যারা বোনের মতো ভালোবাসেনি, পুজোর দিনের ভোরবেলা শিউলি ফুলের গন্ধ জানলা দিয়ে ঢুকে যাদের ঘুম ভাঙায়নি, একবারও যারা জীবনে দেখেনি সূর্যোদয়ে সোনার এই পুরোনো পৃথিবী আমার গাঁয়ে বিয়ের কনের মতো কেমন সুন্দর মধুর হয়ে দেখা দেয়, তাদের কী করে বোঝাব কী আছে সেই গাঁয়ে। ওরা সিনেমায় গিয়ে দেখে এসেছে গ্রাম, জানে না–সে-গ্রাম, না গ্রামের প্রেতচ্ছবি। অন্য দশটা ফালতু ঘটনার মধ্যে দেখেছে, সিনেমা-স্টার অমুক দেবী গাঁয়ের বধূ সেজে সস্তা আর্ট দেখিয়ে কলসি কাঁখে জল আনছেন নদীর ঘাট থেকে। হলদে পাখির ডানায় রঙের মাধুর্য ওরা বুঝবে কী করে? শীতের দিনে নদীর চরের কাশবনে চড়ইভাতি করার আনন্দ অজ্ঞাত ওদের কাছে। ফির্পো কিংবা গ্র্যাণ্ড হোটেলের খানার ওপারে ওরা তো জানে না কিছু।
ফাল্গুন-চৈত্র মাসে গ্রীষ্মের রূপ অপরূপ। ঝরাপাতা মরাফুল উড়ে যায় দমকা বাতাসের মুখে–নবীনের আবির্ভাবের আভাস পেয়ে জীর্ণজরা খসে পড়ে যেন আসনশূন্য করে দেয় তাকে। মৌমাছিদের অবিশ্রান্ত গুনগুনানি শুনতে শুনতে আমের মুকুল বড়ো হতে থাকে। সড়কের ধারে ঢিলের মতো উঁচু জায়গায় দারা! অসংখ্য অনামি বন্য গাছ সেখানে। সাদা ফুলের ছড়া ঝুলে থাকে রাস্তার ওপর। কী মিষ্টি গন্ধ তার! অবহেলিত সেই বৈশিষ্ট্যহীন। গাছগুলোও বসন্তকালে এমআকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। প্রতিসন্ধ্যায় মাঠ থেকে ফুটবল খেলা শেষ করে বাড়ি ফেরবার সময় নীচু ডালের ফুলগুলো আমরা পেড়ে নিয়ে আসতাম লাফিয়ে।
চৈত্রের আগুনে মাটি পুড়ে যেত, জ্বলন্ত আকাশ থেকে নিদারুণ গ্রীষ্ম ঝরে পড়ত মাথার ওপর। এদিক-ওদিক শোনা যেত তৃষ্ণার্ত চাতকের জলপ্রার্থনার করুণ সুর-ফটিক জল, ফটিক জল!
তারপর একদিন কালির দাগ লাগত আকাশের দূরতম কোণায়। তীক্ষ্ণ নীল বিদ্যুৎ ঝলসে উঠত মহাশূন্যে, কড়কড় শব্দে বজের তরুণ কণ্ঠের হুংকার শোনা যেত। কিছুটা সময় বায়ুলেশহীন স্তব্ধতা। নীড়-প্রত্যাশী পাখিদের শঙ্কিত চিৎকার। চারিদিকে কীরকম একটা থমথমানি–তারপরই মনে হত কারা যেন হাজার হাজার ঘোড়া ছুটিয়ে পদ্মার চরের ধূসর বালিতে চতুর্দিক অন্ধকার করে এই গ্রামের দিকেই আসছে। দক্ষিণ দিকের আকাশ চিরে শোঁ শোঁ শব্দ বেরিয়ে আসত। ঘোড়ার খুরের বাজনা গাছপালার মাথার ওপর দিয়ে দ্রুততালে এগিয়ে আসতে থাকত-কাছে…কাছে…আরও কাছে। অবশেষে এসেই পড়ত তারা–প্রচন্ড ঝড়। আকাশে তখন রোদ থাকত না, অথচ অন্ধকারও নয়–মেঘের গা চুঁইয়ে কী এক অদ্ভুত পিঙ্গল আলো টর্চের ফোকাসের মতো লম্বা রেখায় নেমে আসত এদিক-ওদিক, ঝড়ের প্রহারে আকুল আর্তনাদে কেঁদে উঠত বাঁশবন, মড়মড় শব্দে পথঘাট আটক করে উপড়ে পড়ত গাছ, মত্ত বাতাসের মুখে হালকা তাসের মতো উড়ে যেত চালাঘর, তালগাছের পাতায় ঝলসে উঠত বিদ্যুতের আভা। জানলার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকিয়ে, কেন জানি না, আমার শিশুমনে আশঙ্কা হত, রাস্তার ধারে ওই যে ফাঁকা জায়গায় নিঃসঙ্গ একলা দাঁড়িয়ে নারকেল গাছটা, ওটার মাথায় বজ্রপাত হবে। বড়োমার কাছে গল্প শুনেছি, পদ্মায় যে বছর ঝড়ে কালীগঞ্জের স্টিমার ডুবে গিয়েছিল, সেবার আমাদের পুকুরপাড়ের তেমাথা আমগাছে বাজ পড়ে গাছটা ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল, আর সেই থেকেই ওর তিন মাথা।
ঝড়ের বেগ শান্ত হয়ে এলে আসত বৃষ্টি-স্নিগ্ধ বড়ো বড়ো ফোঁটায় নামত বছরের প্রথম বর্ষণ। বৃষ্টিধারায় স্নান করতে করতে আমাদের সেই করমচার গানের কোরাস চলত-কচু পাতায় করমচা, যা বৃষ্টি উড়ে যা। ধূলিলিপ্ত গাছপালার প্রসাধন হত সেই জলে। ভেজামাটি থেকে সোঁদা গন্ধ উঠত। চাতকের পিপাসা বুঝি ওতেও মিটত না, কারণ একটু পরেই আবার শোনা যেত-‘ফটিক জল, ফটিক জল’!
প্রতিবছর বৈশাখ মাসে বাংলাদেশের মাঠেমাঠে কে এক রক্তচক্ষু, পিঙ্গলজটা, রুদ্র সন্ন্যাসী বহ্নিমান চিতাপের সম্মুখে বসে শান্তিপাঠ করে যান। তাঁর গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠধ্বনি শুষ্ক দগ্ধ তৃণ-প্রান্তরের ওপর দিয়ে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটে যায়। তখন জনমানুষের সাড়া পাওয়া যায় না কোথাও, কেবল তন্দ্রাতুর কপোতের ক্লান্তস্বর কোথা থেকে ভেসে এসে যেন সেই গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে মিশে যায়। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে শান্তিনিকেতনের শুষ্ক মাঠে এই শান্তিপাঠরত সন্ন্যাসীকে একজন দেখেছিলেন–সিদ্ধকবির দিব্যদৃষ্টি ছিল তাঁর। কিন্তু আমিও দেখেছি এঁকে, আমাদের বাড়ির সীমান্তবর্তী দিগন্ত-ছোঁয়া বিস্তীর্ণ বাল্লার মাঠে।
তখন আমার বয়স কত বলতে পারব না। তবে এটুকু বলা চলে, ‘পথের পাঁচালী’-র অপুর মতো তখন আমি, আমার নিজের জগতে একজন মস্ত বড়ো কবি, একজন আবিষ্কারক। কাজেই সেই শিশু আমি, যাকে সিদ্ধকবির সঙ্গে বিনাদ্বিধায় এক-আসনে বসানো চলে।…হ্যাঁ, সেই সন্ন্যাসীর অস্পষ্ট স্মৃতি আমার মনে আছে। দুপুর বেলা বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, মায়ের বুকের ওপর থেকে কাশীরাম দাসের মোটা মহাভারতখানা একপাশে কাত হয়ে নেমে এলে, পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তাম। খেজুর গাছের তলায় দাঁড়িয়ে, সভয় দৃষ্টিতে মাঠের দিকে তাকিয়ে মনে হত, ওই দূরে মাঠের ঠিক মধ্যিখানে কীসের যেন ধোঁয়া–আবছা, অস্পষ্ট–শীতের দিনের কুয়াশার ধূসরতা। কী একটা উধ্বমুখী হয়ে কাঁপছে– ছোটো ছোটো ঢেউ–আগুনের শিখা বুঝি! রোদের মধ্যে মিশে গেছে তা, ভালো করে বোঝা যায় না। তার ও-পাশে বসে কে যেন একজন–ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন মূর্তি, দেখা যায় না, চেনা যায় না, কিন্তু অনুমান করতে গিয়ে নিঃসংশয়ে মনে আসে, সে-এক উগ্রদর্শন সন্ন্যাসী, দু চোখে আগুন তাঁর, দয়া নেই, মায়া নেই, ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে যেন ওই চিতার আগুন একলাথি মেরে সমস্ত গ্রামের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে নিমেষে তিনি সব ধ্বংস করে ফেলতে পারেন… ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে থাকতাম, মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করত, শরীর শিউরে উঠত মাঝে মাঝে, কিন্তু এক পা নড়তে সাহস পেতাম না। মনে হত, নড়বার চেষ্টা করলেই তিনি টের পেয়ে যাবেন, আর একবার টের পেলে–!
একদিন অমনি দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে ঝড় উঠেছিল, কিন্তু আমার মনে হয়েছিল, সন্ন্যাসী বুঝি খেপে গেছেন কোনো কারণে। বাতাসে শুকনো মাঠের রাঙা ধুলো উড়ছিল। আমি দেখছিলাম চিতার আগুন পা দিয়ে তিনি লন্ডভন্ড করে দিচ্ছেন। চিৎকার করে বারমুখো ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে বাঁশের কঞ্চির স্থূপের ওপর পড়ে গিয়েছিলাম জ্ঞান হারিয়ে। গলার বাঁ-পাশে অনেকখানি কেটে গিয়েছিল, ক্ষতচিহ্নটা এখনও আছে।
সেসব দিনের ভয়ের কথা মনে পড়লে চোখ সজল হয়ে আসে কেন? ঝাপসা দৃষ্টির সামনে বিস্তীর্ণ বাল্লার মাঠ জলভরা অথই বিলের মতো ছলছলিয়ে ওঠে। আমার ছোটোবেলায় রোজ সন্ধ্যায় আমার গাঁয়ের পোড়োমাঠে আলেয়া জ্বলেছে, ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছটা আগাগোড়া ভয়ের কাঁথা মুড়ি দিয়ে চিরকাল দাঁড়িয়ে থেকেছে, অমাবস্যার রাত্রে কেউ কেউ নাকি নাড়দের পতিত ভিটেয় মেয়েমানুষের হাসি শুনতে পেয়েছে–এসব ভয়-কাহিনি-স্মৃতির দেশে আর একবার যেতে ইচ্ছে করে; মনে হয়, আর একবার বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে হিজলগাছের মাথায় সন্ধের প্রথম তারাটা দেখি, ঝিঁঝির ডাক শুনি বেতের জঙ্গলে।
বর্ষার মেঘান্ধকার বিষণ্ণ দিন কেটে গেলে এসেছে শরৎ। কাস্পিয়ান সাগরের ঘন নীল জল দিয়ে কে যেন ধুয়ে দিত আকাশ। সকাল-বিকেলের রাঙা রোদ তার ওপরে সোনা ছড়াত। মাঠেমাঠে পাকা ধান, সোনালি রং, বৈকুণ্ঠ-লক্ষ্মীর অঙ্গ-আভা যেন। ফসল ভালো হলে মুসলমানরাও বলত, মা লক্ষ্মী এবার ভালো দেছেন গোয়
আমার গাঁয়ে বিলের জলকে ঢেকে রাখত পদ্ম আর শাপলা। খালের পারে, নদীর চরে উচ্ছ্বসিত কাশের বন–সাদা ফেনার সমুদ্র যেন। আশ্বিনের ছুটির বাঁশি বাজত জলে-স্থলে স্টিমারঘাট থেকে যাত্রী নিয়ে একটির-পর-একটি নৌকো এসে ভিড়ত ইছামতীর পারে। গ্রামভরা লোকজন, ঘরে-ঘরে প্রবাস প্রত্যাগতের আনন্দ কলরব। বাংলাদেশের গ্রাম যে চিররূপময়ী কাব্যের নায়িকা নয় তা জানি। সবুজ মাঠ, সোনালি রোদ, পাখির ডাক, পূর্ণিমা রাত্রির জ্যোৎস্নার জলে ধোয়া আকাশের আড়ালে তার যে ঈর্ষা-নিন্দা-দলাদলি, ক্ষুধা-দারিদ্র অকালমৃত্যু পীড়িত বিকৃত বিকারগ্রস্ত রূপ রয়েছে, তাও মিথ্যে নয়। কিন্তু তবু এই পুজোর দিনে একান্ত নিঃস্বের দরজার সমুখেও আঁকা হয় আলপনা, উঠোনে দাঁড়ালে প্রাণখোলা হাসির সঙ্গে কেউ-না-কেউ এসে হাতে দিয়ে যায় দুটো নারকেল-নলেনগুড়ের মিষ্টি। বিজয়ার দিনে ধনী-দরিদ্রনির্বিশেষে বুকে জড়িয়ে সবাই সবাইকে করে আলিঙ্গন। প্রাত্যহিকতার অজস্র গ্লানি বিস্মৃত হয়ে, দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষের কালো চিহ্নগুলো মন থেকে মুছে ফেলে, সমস্ত পৃথিবীকে
বিজয়ান্তে একবার হৃদয়ভরে গ্রহণ করা ছিল পূর্ববাংলার চিরাচরিত রীতি। আমার গাঁয়ের তেমনি পরিবেশ আর জীবনে কোনোদিন দেখতে পাব, তা যে কল্পনার অতীত।
আমাদের চন্ডীমন্ডপে প্রতিমা তৈরি হত। একমেটে, দো মেটে, মাজাঘষা–তারপরে রং। পুজোর কাছাকাছি তিনজন কুমোরের অনেক রাত অবধি লণ্ঠন জ্বেলে কাজ চলত। ঘুমের ঘোরে অবস্থা কাহিল হয়ে না পড়া পর্যন্ত ছেলে-মেয়েদের ভিড় কমত না। নানারকম বায়না নিয়ে তারা বসে থাকত।
যোগেন দা, এই যে দেখো, আমার পুরোনো পুতুলটায় একটু রং চড়িয়ে দেবে–তোমার ওই দুর্গার চুড়ার সোনালি রংটা?
আর এই যে আমার ঘোড়াটা যোগেনদা, ঠ্যাংটা ভেঙে গেছে, একটু জুড়ে দাও না ওই এঁটেল মাটি দিয়ে।
যোগেনের কোনোদিকে তাকাবার অবসর নেই, মুখে হু-হ্যাঁ চালিয়ে সে তুলি টানতে থাকত।
এই ছাওয়ালপান, কামের সময় প্যানপ্যান কইরো না।–উঠোনের ওধার থেকে ছেলেদের ধমক দিত ইয়াদ আলি। প্রতিমা-সজ্জা দেখার শখ ছেলেদের অপেক্ষা কিছুমাত্র কম নয় তার। মুসলমানপাড়ার দোর্দন্ড প্রতাপশালী সর্দার সে। পঞ্চাশের ওপরে বয়স। মাথায় কাঁচা-পাকা চুলের বাবরি। প্রচুর পান খেয়ে খেয়ে দাঁতগুলো সে করেছে পাকা তরমুজের বিচির মতো কুচকুচে কালো। চাষাবাদ আর দস্যুবৃত্তি তার উপজীবিকা। মানুষ খুনের ঐতিহ্যবাহী বংশের অধস্তন পুরুষ সে। দু-চারটে লাশ সে নিজেও যে মাটির নীচে পুঁতে দেয়নি এমন নয়।
তুমি চ্যাংড়াদের কথায় কান দিয়ো না পালমশায়, মন লাগিয়ে চিত্তির করো,-ই সব ভগমানের কাম।–যোগেনকে পরামর্শ দিত ইয়াদ আলি। কিন্তু গ্রামে থাকতেই দেখে এসেছি, সে ইয়াদ পালটে গেছে। আনসার বাহিনীর নায়ক সে। হিন্দুর দেবতার নাম মুখেও আনে না, ইসলামের চমৎকার ব্যাখ্যা করে।
চলতি রাজনীতির সঙ্গে এ গ্রামের বরাবরই যোগ ছিল। পোড়োভিটের গভীর জঙ্গলে বেশি রাতে গোপনে মিটিং হত। তারপরেই শুনতে পাওয়া যেত, আট-দশ মাইল দূরে সাহাদের পাটের আড়তের ক্যাশ লুঠ হয়েছে। মহকুমা শহর মানিকগঞ্জ অনুশীলন পার্টির নেতা বিপ্লবী পুলিন দাসের অন্যতম কর্মকেন্দ্র, আর ঢাকেশ্বরী কটন মিলের ভূতপূর্ব ম্যনেজিং ডিরেক্টর রজনী দাস ছিলেন মানিকগঞ্জ শাখার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। এ গ্রামের কয়েকটি তরুণ সেখানে নিয়ত যাওয়া-আসা করতেন। সেই সূত্রে আমাদের বাড়ি পুলিশে সার্চ করেছে একাধিক বার; কাকাদের গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। সে-সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যায়াম এবং লাঠিচালনা শিক্ষার সমিতি স্থাপিত হয়েছিল অনুশীলন পার্টির নেতৃত্বে। ঢাকায় অনুষ্ঠিত সারাবাংলার লাঠিয়ালদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এ গ্রামের ছেলে সুধীর দত্ত অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়নের গৌরব অর্জন করেছিলেন। দীর্ঘকাল পূর্বে তিনি মারা গেছেন। এ জন্যে আক্ষেপ করি না। সেকালের বিপ্লবীকে আজ শরণার্থীদের মধ্যে দেখতে হচ্ছে না–নিঃসন্দেহে এ সৌভাগ্য নয় কি? বিয়াল্লিশ সালের অগাস্ট মাসেও স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে ছিল এখানে। নিরুদবিগ্ন পল্লিজীবনের অনাবিল শান্তিতে লেগেছিল প্রচন্ড দোলা। গাঁয়ের কাঁচাসড়ক ধরে ভারী বুটের শব্দ করতে করতে আসতে দেখেছি সঙিনধারী পুলিশ।
গ্রামের লোকের, বিশেষত যুবকদের চেষ্টায় গড়ে উঠেছিল প্রকান্ড পাবলিক লাইব্রেরি, থিয়েটারের ‘এভার গ্রিন’ ক্লাব। ক্লাবের ছিল সম্পূর্ণ নিজস্ব ষ্টেজ। প্রতিবছর পুজোর সময় তিন রাত্রি অভিনয় বাঁধা ছিল, এবং অভিনেতারা প্রায় সকলেই ছিলেন ঢাকা কিংবা কলকাতার কলেজের ছাত্র। ক্লাব-লাইব্রেরি যাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তাঁরা জীবনের জটিলতা আর জীবিকার ধাঁধায় জড়িয়ে পড়লে এর নায়কতা এসেছিল আমাদের হাতে। ভবিষ্যতে একদিন হয়তো আমাদের কাছ থেকে কনিষ্ঠদের হাতে উত্তীর্ণ হয়ে যেত এই নেতৃত্ব। কিন্তু তার আগেই যে গ্রাম ভেঙেছে, কে কোথায় ভেসে গিয়েছে জোয়ারের মুখে কে জানে!
গ্রীষ্মকালে চারদিক যখন শুকনো খটখটে, ক্লাবের সভ্যদের উৎসাহে প্রতিবছরই একবার করে সে-সময়ে গ্রামের স্বাস্থ্যোদ্ধার করা হত। পুকুর থেকে, নদী থেকে কচুরিপানা টেনে তুলে শুকিয়ে আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিতাম আমরা। সমবেত আক্রমণের মুখে অবাঞ্ছিত ঝোঁপজঙ্গল নিঃশেষ হয়ে যেত। দুর্গম রাস্তা সংস্কারের উদ্দেশ্যে চুপড়ি-কোদাল নিয়ে অভিযান চলত–মাটির বোঝা বইতে গিয়ে টনটন করত আমাদের মাথার চাঁদি।
দু-বছর আগে এক অপরাহ্নে ইছামতী পাড়ি দিয়ে আমার জন্মভূমি খেরুপাড়া ছেড়ে চলে এসেছি। নিজের বাড়ি বিদেশ হয়েছে, ঘরে ফেরার পথে গজিয়েছে বিষাক্ত কাঁটা। এ জীবনে খেরুপাড়ার কালো মাটির পথে বুঝি আমার পায়ের চিহ্ন আর পড়বে না। কিন্তু যদি এ অনুমান ব্যর্থ হয়, কখনো যদি গঙ্গা-পদ্মা ফের নতুন রাখিবন্ধনে বাঁধা পড়ে, তা হলে কি আমি আবার তেমনিভাবে ফিরে পাব আমার সেই হারানো খেরুপাড়াকে?
অবিশ্বাস গাঢ় হয়ে আসে, সংশয়ে দুলতে থাকে মনটা। আশার সার্থকতায় ফিরে পাওয়া গ্রামে পৌঁছোল কেউ যদি হঠাৎ এসে খবর দেয়, ও পাড়ার যারা প্রাণের মায়ায় সীমান্তপারের দেশের উদ্দেশে যাত্রা করেছিল, মাঝপথ থেকে তাদের আর খবর নেই কিংবা যদি কেউ বলে, পাশের গ্রামের এক অসহায় গৃহস্থ পরিবারের নতুন বউ কোনো উপায় না দেখে একগোলা আফিম মুখে পুরে ঠাকুরের পটের সামনে চুপচাপ মুখ বুজে শুয়েছিল, সে আর উঠে বসেনি–অথবা যদি শুনতে পাই, আমাদেরই প্রতিবেশীর এক কুমারী মেয়ে, আমাদের পুকুরধারের কৃষ্ণচূড়া গাছটা ফাল্গুন মাসে যখন অসংখ্য রক্তমঞ্জরিতে লালে লাল হয়ে ওঠে, তারই ডালে চূড়ান্ত অপমান থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্যে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলেছিল, তখন আমার চোখ ফেটে যে জল আসবে, সে কি পুনর্মিলনের আনন্দে? আমি যদি অসহ্য চাঞ্চল্যে পথের ধুলোয় লুটিয়ে পড়ি, তা কি অদৃষ্টের দেবতাকে সকৃতজ্ঞ প্রণাম জানাবার জন্যে? সময়ের গতি দুর্বার, জীবন অস্থির–পদ্মপাতায় জলবিন্দু টলমল। যা হারালাম, যা ফেলে এলাম, অনন্ত-অতীত তাকে গ্রাস করে নিল, কোথাও তার আর সন্ধান মিলবে না।
আকাশে বর্ষার মেঘ, বিচ্ছিন্ন কান্নার সুর। কিন্তু সে-সুরে তো হৃদয় ময়ূরের মতো পেখম বিস্তার করে নাচে না। প্রাসাদের শিখর থেকে কারও কালো চুলের ঢেউ আকাশ ঢেকে ফেলেছে–এ কল্পনাতেও মন তো এগোয় না। আমি দেখতে পাচ্ছি, এই মেঘেরই ছায়া পড়েছে ইছামতীর জলে। তারই তীরে দাঁড়িয়ে জনহীন বিপন্ন খেরুপাড়া গ্রাম। অহল্যার পাষাণ-জীবন তার। মুক্তির অপেক্ষায় চলছে অপমৃত্যুর প্রহর গণনা। তবু কেন জানি না, প্রবল প্রত্যয়ে কবিগুরুর সেই অমৃতময়ী আশার বাণী বার বার মনে আসে,
মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই
এই সূর্যকরে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয়-মাঝে যদি স্থান পাই।
তেমনি স্থান কি পাব না আমরা?
সংগ্রামের নায়ক নিয়তির সঙ্গে দ্বন্দ্বে পরাজিত হয়েছে। তার রথচক্র গ্রাস করেছে মেদিনী, অন্যায় চক্রান্তে বিপর্যস্ত সে। কিন্তু তার পৌরুষ লুপ্ত হয়নি, বীর্যের বিনাশ নেই, আদর্শ অমর। দিগন্তের নিকষ অন্ধকারে দৃষ্টি চলে, কিন্তু কার যেন পদধ্বনি শোনা যায়! অন্ধকারে যবনিকা থরথর করে কেঁপে ওঠে।
.
ধামগড়
‘এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা বলে ভাসা তরী’–গানটি কত উৎসবে কতবার যে গেয়েছি তার ঠিক নেই। কবিগুরুর মহাবাণী শুনে প্রাণে শক্তি পেয়েছি সত্য, কিন্তু আমাদেরও যে সর্বস্বত্যাগী হয়ে ‘জয় মা’ বলে এমনিভাবেই তরি ভাসাতে হবে অনির্দিষ্টতার পথে তা আগে কি কোনোদিন ভাবতে পেরেছিলাম? ভারত স্বাধীন হবে, আমরা সুখীসচ্ছল হব, বাঙালির ঘর ভরে উঠবে আবার ধন-ধান্যে, পুজো-পার্বণে–এই স্বপ্নই তো দেখেছি রাত জেগে জেগে! কিন্তু তার বদলে আমরা হলাম নির্বাসিত, অসহায় পাখির মতো বিপদগ্রস্ত।
মনে পড়ছে প্রায় বারোবছর আগে আমাদের গ্রামের এক বাড়িতে একমাত্র পুত্র দেবেন মারা গেলে আমার ঠাকুমা দুঃখ করে বলেছিলেন,–‘আহা, সারদার ভিটেয় আর প্রদীপ দেবার কেউ রইল না!’ কিন্তু আজ সমস্ত পূর্ববাংলার প্রতি হিন্দু-পরিবারে ছেলে থাকতেও প্রায় ভিটেতেই প্রদীপ দেওয়ার কেউ নেই।
নারায়ণগঞ্জ থেকে মাইল তিনেক দূরে আমাদের গ্রাম ধামগড়। স্টিমার বা নৌকো যাতে খুশি যাওয়া যায়। তবে নৌকোতে গেলে দেড় ঘণ্টা আর স্টিমারে গেলে লাগে আধঘণ্টা। ছাত্রাবস্থায় এ দুটোর কোনোটাতেই মন সরত না–সামান্য সময় অপচয়ও ছিল তখন প্রবাসীমনের পক্ষে অসহ্য। বাঁধনছেঁড়া মন মুহূর্তে বাড়ি পৌঁছোবার জন্যে পাগল হয়ে উঠত। স্টিমারে গেলে সারং, সুখানী, ড্রাইভার কর্মচারীদের দেওয়া খাবার জুটত প্রচুর। এ-উপহার জুটত বাবার সম্মানে, তিনি তখন সোনাচোরা ডকের ডাক্তার। তাই ছোটোবাবু (আমি) তাদের আপনার জন, তাকে আদর করার অর্থ তার পিতাকে সম্মান দেখানো। নৌকোতে গেলে যেতাম চারার গোপে। আমাকে দেখামাত্রই জনদশেক মাঝি হুমড়ি খেয়ে এসে দাঁড়াত চারপাশে। তারা সবাই প্রায় মুসলমান। কার নৌকোয় উঠব ভেবে ঠিক করতে পারা যেত না। যাকে প্রত্যাখ্যান করব তারি তো হবে অভিমান! তবুও কেউ কেউ আমার শোচনীয় অবস্থাকে আরও সঙিন করার জন্যেই ছোঁ মেরে নিয়ে যেত বাক্স–বিছানা-সুটকেস। তারপর সমস্বরে আহ্বান জানাত—’আইয়েন ছোড ডাক্তারবাবু আমার নায়ে, ছোত কইরা যাইতে পারবেন!’ পিতার খেতাব আমার কপালে যেন উত্তরাধিকার সূত্রেই জুটেছিল! এরপর কাঁচুমাচু মুখে একজনের নৌকোয় গিয়ে হয়তো উঠতাম–যারা সুটকেস ও বিছানা নিয়ে গিয়েছিল তখন তারা তা হাসিমুখেই ফিরিয়ে দিয়ে যেত সে-নৌকোতে। আমি সাধারণত যার নৌকোয় যেতাম, মনে পড়ে, সে গান গাইত চমৎকার। রসুল মাঝি বলেই সে পরিচিত ছিল। আমাদের কাছে। নৌকো ছেড়ে সে ডান হাতে দাঁড় টানত আর বাঁ-হাতে হুঁকো ধরে টানত কড়া তামাক। তামাক খাওয়া শেষ হলে ছোট্ট একটা কাশির পর উদাত্ত কণ্ঠে গান ধরত সে,
গুরু আর কতদিন থাকবা ফারাক, পাইনা তোমার দ্যাহা,
কত দুঃখ সইলাম দরায়, নাইকো ল্যাহ জোহা।
গুরুভজা রসুলমাঝি গান গেয়ে চলেছে আনমনে একটানা। অপূর্ব পরিবেশের মধ্যে দূরে দেখা যাচ্ছে শীতলক্ষ্যার পুবপাড়ে ঢাকেশ্বরী মিলের চিমনি, বসু গ্লাস ওয়ার্কসের কারখানা। পশ্চিম দিকে পাটের কল দু-নম্বর ঢাকেশ্বরী মিলের চোঙা, লক্ষ্মীনারায়ণ মিল আর চিত্তরঞ্জন মিলের খাড়া-উঠে-যাওয়া চিমনির শ্রেণি অবিরাম ধোঁয়া উদগিরণ করে চলেছে যেন মানুষের ইতিহাসকে কলঙ্কমলিন করার উদ্দেশ্যেই!
আজ বেশি করে মনে পড়ছে রসুল মাঝির ভারি খোলা গলার ভক্তিমূলক সেসব গান। শীতলক্ষ্যার জলে তার দাঁড়ের ছপছপ শব্দ আমাকে যেন অন্য কোনো জগতে নিয়ে যেত। সেদিনকার গোধূলিবেলায় বৈরাগীমন যেমন নিমেষে চলে যেত অন্য জগতে আজ রূঢ় বাস্তবময় পরিবেশে দেহও স্থানান্তরিত হয়েছে অন্যদেশে। চিরদিনের জন্যেই কি হারিয়েছি শীতলক্ষ্যার শান্ত করুণ মিনতিভরা রূপকে, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা জননী জন্মভূমিকে!
মাতৃভূমিকে ছেড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ফেলে এসেছি সমস্ত ঐশ্বর্য ও সম্পদকে। অকৃত্রিমভাবে বুঝতে পেরেছি স্বাধীনতা আমাদের দেশে পরাধীনতার অভিশাপ নিয়েই দেখা দিয়েছে। অমাবস্যার ঘোর কালরাত্রির মধ্যে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি বলেই জীবনেও দেখা দিয়েছে অমাবস্যার করাল ভয়াল মূর্তি! রাত্রি প্রভাতের কত দেরি কে বলে দেবে? মহামনীষীরা স্তোক দিয়েছেন wait for the morning owl! কিন্তু শীতলক্ষ্যার তীরে আবার পূর্বাকাশের সূর্যোদয়ের রক্তরাগরেখায় গোধূলির দেখা পাব কি না জীবনে কে জানে।
সন্ধেবেলায় দেখতাম একহাতে প্রদীপ আর অন্যহাতে ধুনুচি নিয়ে প্রাঙ্গণপাশে তুলসীমঞ্চে মা গলায় আঁচল দিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করছেন। দেবতার কাছে তিনি কী প্রার্থনা করতেন জানি না, কিন্তু আজকের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে স্বচ্ছন্দে বলতে পারি, তাঁর ভীরু হৃদয়ের উজাড় করা প্রণাম এবং প্রার্থনা পূর্ণ হয়নি। জীবনকে বিপদমুক্ত করার সব আবেদনই ব্যর্থ হয়েছে আমাদের। একা একা থাকলেই মনে পড়ে যায়, গ্রামের নিস্তব্ধ দুপুরে জামের ডালের ওপর বসা ঘুঘু দম্পতির একটানা সুর, আজও হয়তো শুনতে পাওয়া যায় সে-সুর, কিন্তু সে ডাকে কটা মানুষের মন সাড়া দেয় এখন?
দুরন্ত দুপুরের ছবি যেন ক্রমাগত চোখের সামনে ভেসে উঠছে আজ। মনে হচ্ছে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, সামনে সবুজ মাঠের বিস্তীর্ণ ফসল ফলার ছবি। কোনো জমিতে ধানগাছ বাতাসের সঙ্গে মাথা দুলিয়ে নড়ছে সবুজ যৌবনকে চারিদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে, আবার কোনো মাঠে অজস্র পাটচারার সমারোহ। সব খেতে উবু হয়ে বসে মাথায় টোকা দিয়ে খেত নিড়িয়ে দিচ্ছে অখন্ড মনোযোগ সহকারে কৃষকের দল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে আবার গানও হচ্ছে–কোহিল ডাইক্কো না ডাইক্কো না এই কদম্ব ডালে। জমি থেকে উঠছে কুন্ডলী কেটে ধোঁয়া, খড় পাকিয়ে লম্বা দড়ি করে গোড়ায় আগুন দেওয়া হয়েছে তামাক খাওয়ার জন্যে। সংকীর্ণ আল দিয়ে হেঁটে চলেছে ক্লান্ত ‘বি’ শিফটে ছুটি পাওয়া শ্রমিকদল। কারুর মাথায় ছাতা, কারুর মাথায় বড়ো বড়ো কচুপাতা! কেউ যাবে রানিঝি, কেউ জাঙাল, কেউ বা পুবদিকের নমশূদ্র পাড়ায়। কারুর গন্তব্যস্থল মালিবাগ কারুর বা আরও দূরে লাঙলবন্ধ। ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমপাড়ে হিন্দুতীর্থ লাঙলবন্ধ খুব কাছে নয়।
ছোটোবেলায় মায়ের সঙ্গে অষ্টমীস্নান করতে কতবার এই লাঙলবন্ধে গিয়েছি। দূরত্ব ছিল মাইল-দুই পথ। গ্রামের গৃহিণীরা যেতেন পাল্কি চেপে, কিন্তু মাকে কোনোদিন পাল্কিতে যেতে দেখিনি। তিনি বলতেন, “এইটুকু পথ চলতে না পেরে পাল্কিতে চড়ে তীর্থ করতে হয় যদি, তাহলে সে-তীর্থের ফল কী? ওরকম তীর্থ করার চেয়ে না করাই ভালো। তাই মুখ কালো করে আমাকেও হাঁটতে হত তাঁর সঙ্গে। মায়ের হাঁটা বড়ো আস্তে, ভোর চারটের সময় যাত্রা করেও তাই আমরা পৌঁছোতাম রোদ উঠে যাওয়ার পরে। আমাকে হাঁটতে হত না বড়ো একটা, কেননা সঙ্গে থাকত দুজন প্রজা। একজন মামুদ আলি আর একজন কালীচরণ। চলার মাঝখানেই হঠাৎ থেমে বিষণ্ণ মুখে মায়ের আঁচল চেপে কাঁদো কাঁদ স্বরে বলতাম—’মা, পা বড্ড কনকন করছে!’ মা জবাব দেওয়ার পূর্বেই চতুর মামুদ আলি বুঝে ফেলত আমার চালাকি। আকর্ণ হাসিকে বিস্তৃত করে মায়ের হয়ে সে-ই বলত—’আইয়ো আইয়ো, তোমার চালাকি বুঝি বুজি না ছোট্টবাবু!’ এই বলে স্বচ্ছন্দে সে তুলে নিত ঘাড়ে।
মাঠে মাঠে রাস্তা কিছু কম, তাই আমরা আল ধরে এগিয়ে যেতাম। দেখতাম অজস্র ভক্ত তীর্থযাত্রী ভক্তির অর্ঘ্য নিয়ে ছুটে চলেছে তীর্থসলিল স্পর্শ করতে। পুণ্যকামী বাঙালির এই চিত্র সর্বত্রই এক। চলতে চলতে চোখে পড়ত শস্যশ্যামলা মাতৃভূমির লুকোনো সম্পদ। ধান-পাট-মেঠোকুমড়োয় মাঠ পরিপূর্ণ, কোথাও লাল লঙ্কায় লালে লাল। মেলার পথে দোকানদাররা নিয়ে চলেছে ধনে-জিরে-তেজপাতার তৈজসপত্র। আবার কারুর মাথায় খই মুড়কি-ডবল বাতাসার গুরুভার। যাত্রীরা এইসব জিনিস কিনে আনবে বাড়ি ফেরার পথে। মামুদের কাঁধে গদিয়ান হয়ে মনটা বেশ স্ফুর্তি-স্ফুর্তিই ঠেকত।
ভোরের বাতাসে ভেসে আসছে মেলার হট্টগোল, খোলের মিঠে আওয়াজ, কীর্তনের অসমাপ্ত কলি। হঠাৎ শুনতে পেলাম দূর থেকে কে যেন হাঁকছে ‘বিশু বাই’ করে। চকিতে ঘাড় ফিরিয়ে দেখি উজ্জ্বল দাঁত বের করে হাসছে গঙ্গা। বাল্যবন্ধু গঙ্গা, সহপাঠী গঙ্গা অবাঙালি গঙ্গা। জন্মেছে আমাদের গ্রামে, বাড়ি মুঙ্গের জেলার এক পল্লিতে। তার বাবা রঙ্গলাল চৌকিদার। গঙ্গার ভাগ্যে কোনোদিন জন্মভূমি দেখার সুযোগ হয়নি, সে আমার গাঁয়েরই ছেলে, তাকে দেখে কাঁধ থেকে নামতে চাইলাম, কিন্তু মামুদ ধমকে বলে উঠল–না ছোটোবাবু আরাইয়া জাইবা, বিরের মইদ্যে লামতে দিমু না– কী করি উঁচু থেকেই গঙ্গার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগিয়ে চললাম। মেলায় পৌঁছে দেখি স্নান সেরে মেয়েরা কাঁখে বা মাথায় নতুন হাঁড়ি কিনে নিয়ে যাচ্ছে। কৌতূহলী শিশু সেদিন জিজ্ঞেস করেছিল কাঁধের ওপর থেকে—’মামুদ ভাই, হাঁড়ির মধ্যে কী নিয়ে যাচ্ছে ওরা?’ মামুদ বিজ্ঞের মতো কমকথায় উত্তর দিয়েছিল—‘পুইন্যি!’
কলকাতার পথে চলতে চলতে শুনতে পাই বেতার শিল্পীদের ভাটিয়ালি, রামপ্রসাদি, বাউল, শ্যামাসংগীত এবং আরও কতরকম ভক্তিমূলক গান। এসব শুনলেই মনটা আকুলি বিকুলি করে ওঠে শৈশবে দেখা কিশোরী বাউলের কথা ভেবে। কিশোরী বাউলের সেই টানাটানা চোখ দুটো, আজও আমাকে সম্মোহিত করে রেখেছে যেন! ভুলতে পারিনি তার সৌম্য-সুন্দর ঢলঢলে মুখখানি। পরনে গেরুয়া, এককাঁধে ঝুলি আর এক কাঁধে সারেঙ্গি। মাসান্তে দেখা পেতাম তার ঠিক দুপুরবেলায়। তার গান শোনার জন্যে উদগ্র হয়ে থাকতাম নির্দিষ্ট দিনে। কিশোরী বাউল তার সারেঙ্গির ওপর ছড় ঘষতে ঘষতে ঢুকত লাল সুরকি-ঢালা পথ বেয়ে। বেরিয়ে বারান্দায় আসার সঙ্গে সঙ্গে কিশোরী প্রণাম করত আমাকে। তারপর একটুখানি বসে গান ধরত—’আলোকের পূর্ণ ছবি আর কতদিন রবে দূরে। আজ কিশোরী কোথায় জানি না, তবে তার সঙ্গে দেখা হতেও পারে একদিন।‘ কারণ কিশোরীই বলেছিল আমাকে—’বাবু, বাংলাদেশের যেখানেই থাকেন না কেন, এই কিশোরীর সঙ্গে আপনাদের দেখা হবেই।‘
কলকাতার বর্ষা দেখে আমার ছেড়ে-আসা গ্রামের বর্ষার রূপ মনে পড়ে। ডোবা নালা সব জলে টইটম্বুর। পুকুরের পাড় ভেঙে ছুটছে জলের স্রোত–সেই স্রোতের একপাশে বঁড়শি নিয়ে মাছ শিকারে ওত পেতে আমি বসে। শোঁ শোঁ শব্দে জল যাচ্ছে মাঠের ওপর দিয়ে। আজ মনে হয় সেই অশ্রান্ত বাঁধভাঙা জলের কল্লোলধ্বনি আর কিছুই নয়, বিপর্যস্ত মানুষের হাহাকার যেন–জলস্রোতের শিহরন আজকে আমার মনে জনস্রোতের বিহ্বলতার কথাই মনে করিয়ে দেয়। ঘরছাড়া মন জলস্রোতের সঙ্গে জনস্রোতের সাদৃশ্য কী করে খুঁজে পেল জানি না। জল ঝরে পড়ার শব্দে শিশুমন যেমন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠত, আজকে কেন জানি না হৃদয়তন্ত্রীতে সেই শব্দ ব্যথার রেশ লাগায়। হয়তো ব্যথাতুর মন প্রকৃতির মধ্যে বেদনাবিধুর আবেশটিকেই গ্রহণ করে। মেঘের খেয়ায় খেয়ায় মন উদাসী।
বর্ষার জলে মাঠ থই থই করছে, পাটগাছগুলো কাটা হয়ে গেলেও ধানগাছগুলো খাদ্যভারে বাতাসে দোল খাচ্ছে জলস্রাতের মুখে। জলের মধ্যে মাথা তুলে রয়েছে একটা কদম গাছ ফুলসম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে। পাতার গা বেয়ে জল ঝরছে টিপ টিপ শব্দে। সামান্য শব্দ সামান্য দৃশ্য যে মনকে এতখানি ভাবিয়ে তুলতে পারে কোনোদিন তা দুঃখ না পেলে বুঝতে পারতাম না। মনকে উৎসুক, উদগ্র করেছে সংকট–আজ বুঝতে পারছি সংকট না এলে ইতিহাস সৃষ্টি হয় না। কিন্তু প্রাণঘাতী এ ইতিহাস আমাদের জীবনকে মূলধন করে না গড়লে কী ক্ষতি হত ভবিষ্যতের?
জীবনকে ঘিরে রয়েছে দীর্ঘ দুঃস্বপ্ন। রাত্রিকে পাড়ি দেওয়ার শক্তি কোথায় পাব? প্রতি বাস্তুহারার চোখের জল যেন অশান্ত পদ্মার উন্মত্ততার কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে অহরহ। যাদের ছিল ঘর তারা আজ মুক্ত আচ্ছাদনহীন বিস্তৃত ভূমিতে নিরালম্ব হয়ে রাতের পর রাত কাটাচ্ছে। এক প্রদেশ থেকে এক এক দলকে বিতাড়িত করা হচ্ছে অন্য প্রদেশে। ভয় হয় এ ধরনের বিতাড়নে ক্ষয়িষ্ণু বাঙালি ইতিহাসের পাতায় স্থান পেয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকদের থিসিসের খোরাক হয়ে দাঁড়াবে না তো শেষে? যাযাবর জাতিরা মাটিকে কেন্দ্র করে তবেই সভ্য হয়েছিল একদিন, আর আমরা মাটিকে হারিয়ে হলাম যাযাবর।
.
আনরাবাদ
দেশের কথা নির্জন জীবনে আজ নানাভাবে বেশি করে মনে পড়ছে। মনের ছায়াতলে বিনা ভাষায় বিনা আশায় আমার ছোট্ট নিরালা গ্রামখানি বার বার মাথা তুলে দাঁড়িয়ে পরমুহূর্তে যাচ্ছে মিলিয়ে। দেশজননীর কথা, জন্মভূমির কথার অর্থই হল অজান্তে নিজের কথা। শিশু শুধু নামের নেশাতেই ডাকে, সে যে কথা বলতে শিখেছে এটাই সেখানে বড়ো কথা। সেইরকম আমার গ্রামের কথা বলাও একটা সুখস্মৃতি। আজ প্রাকৃতিক সুষমামন্ডিত আমার সেই ছোটো গ্রামখানিই মনের মণিকোঠায় পূর্ণতা লাভ করেছে।
বসন্তের প্রতীক কচি কিশলয়, ফোঁটা মুকুলের মিষ্টি গন্ধ, লতাগুল্মের ছায়ায় বসা দোয়েল শ্যামার ডাক মনকে কেন জানি না লোভার্ত করে তুলছে এই ইটকাঠ-ঘেরা অকরুণ মহানগরীর কারাগারের মাঝখানে। এখানে রাত্রির কোনো মনোহারিণী রূপ নেই, রাতের কলকাতা ভয়ংকরতারই প্রতীক! কিন্তু আমার সেই ছেড়ে-আসা গ্রামের অন্ধকারের রূপও চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ঝিল্লিমুখরিত অন্ধকার রাত্রে শেয়ালের ডাক এক নিমেষেই চমৎকার একটি গ্রাম্য পরিবেশ সৃষ্টি করে তোলে। একথা বুঝতে পারছি অনেক দূরে এসে এবং চিরতরে গ্রামকে প্রণাম করে আসার পর। নগরজীবন বনাম গ্রামজীবন সম্বন্ধে শৈশবে একবার আমাদের মাস্টারমশাই রচনা লিখতে দিয়েছিলেন। স্পষ্ট মনে পড়ে সেদিন আমি নগরের রূপটির বাইরের চাকচিক্য দেখে তার দিকেই ভোট দিয়েছিলাম। আজ আক্ষেপ হয় গ্রামকে সেদিন অবহেলা করেছি বলে, গ্রামকে সেদিন চিনিনি বলে! শৈশবের সেই বোকামির জন্যে দূর থেকে পরবাসীর মতই ভক্তিভরে তাকে প্রণাম জানিয়েছি এই বলে—’ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা।‘
ঢাকা জেলার কুখ্যাত রায়পুরা থানার অন্তর্গত আনরাবাদ আমার গ্রাম। গ্রাম হিসেবে ইতিহাসবর্জিত, অখ্যাত, অজ্ঞাত হয়তো অন্যের কাছে। কিন্তু তবু সে যে আমার আরাধ্য জন্মভূমি! মাইল তিনেক দূরে মেঘনা, একমাইল দূরে রেল স্টেশন, দু-মাইল দূরে থানা আর ষাট মাইল দূরে কাছারিবাড়ি। আম, জাম, কাঁঠাল, তাল, বাঁশ, বেত আর বর্ণালি গাছের ছায়াঘেরা আনরাবাদ নিস্তব্ধ। কোলাহলমুখর জীবন থেকে মুক্তি চাইলে আনরাবাদ আজকের বিংশ শতাব্দীর কেজো মানুষদের শান্তিময় পরিবেশের সন্ধান দিতে পারে।
আমাদের গ্রামে বাস করতেন অনেক বড়ো বড়ো পন্ডিত। বিদ্যারত্ন, বিদ্যাভূষণ, বিদ্যালংকার, স্মৃতিতীর্থের তীর্থভূমি বললেও এ গ্রামকে বাড়িয়ে বলা হয় না। দূর-দূরান্তর থেকে লোক আসত এই গ্রামের পন্ডিতসমাজের কাছে বিধান নিতে; তাঁদের মুখের কথাকে। আমরা বেদবাক্য মনে করতাম। টোল ছিল অনেকগুলো, ছোটোবেলায় দেখেছি সেখানে বহু বিদ্যার্থী আসত বিদ্যার্জনে। প্রাচীন ভারতের মুনি-ঋষিদের আশ্রমের কথা শুনেছিলাম ঠাকুরমার মুখে, এগুলো দেখে সেই আশ্রম-স্মৃতি যেন চোখের সামনে উঠত ভেসে।
গ্রামবাসীর প্রয়োজন ছিল অত্যন্ত অল্প, তা ছাড়া, মালিন্য যারা আনে তেমনি সব বড়ো বড় প্রতিষ্ঠান আমাদের গ্রাম থেকে দূরে থাকায় মিথ্যে গোলমালের হাত থেকে আমরা একরকম মুক্তি পেয়েছিলাম। থানা-পুলিশের দূরত্ব, কোর্ট-কাছারির দূরত্ব একটু বেশি হলেও শান্তিভঙ্গ কোনোদিন হয়নি। সেই শান্তি-শৃঙ্খলার কোনো বালাই আজ আর নেই সেখানে। তবু আজও মরুভূমির মধ্যে আমার গ্রামটি দাঁড়িয়ে আছে ওয়েসিসের মতো।
পাকিস্তান হবার কিছুদিন পরে দেখে এসেছি আমার গ্রামকে–মায়ের আমার সে রূপ গেল কোথায়? অশ্রু রোধ করতে পারিনি তাঁর হতশ্রী দেখে। ঝাড়ের বাঁশ বাড়ি ফেলেছে ঘিরে, যে আঙিনায় বারো মাস থাকত আলপনার ছাপ সে ছাপ কবে মুছে গেছে। আঙিনায় গজিয়েছে মানুষ-সমান বুনোঘাস। ঘরদোর খাড়া রয়েছে বটে, কিন্তু সমস্তই শ্রীহীন– প্রেতপুরীর মতো ভয়াবহ হয়ে উঠছে সমস্ত গ্রামটি! বিষাদবিধুর নিস্তব্ধতা শ্বাসরোধ করে তুলছিল আমার। আমার দেশজননীর এমন রূপ কোনোদিন দেখব তা স্বপ্নেও ভাবি নি। এখন সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় নিশাচর শ্বাপদ এবং দ্বিপদের অভিযান। কোনো উপায় যাদের নেই তারা সেইসব অত্যাচার সহ্য করে আজও মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছে সে গাঁয়ে। প্রকৃতির শ্যামচিক্কণ আঁচল দিয়ে যে গ্রাম ছিল ঢাকা তার এ ধরনের শান্তিভঙ্গ যারা করেছে তাদের কি প্রকৃতিদেবী কোনোদিন ক্ষমা করতে পারবেন?
সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর আমি জননীর অঞ্চলতলে ছিলাম নির্বিঘ্নে নির্ভাবনায়। তাই বুঝিনি গ্রামের শান্তি, জননীর স্নেহ কতখানি নিবিড় হতে পারে। বিগত জীবনে সুখে-দুঃখে বিপদে-সম্পদে মায়ের যে অভয়বাণী অথবা স্নেহ-সুনিবিড় শীতল ছায়ার আস্বাদ পেয়েছি তা আজ একসঙ্গে ভেসে এসে বিষাদখিন্ন মনকে শৈশব-কৈশোর-যৌবনের পরমানন্দ রূপটি মনে করিয়ে দিয়ে অসহ্য ব্যথায় হৃদয়তন্ত্রীকে বিকল করে দিচ্ছে যেন। আজ সেদিনের স্মৃতিকে স্পর্শ করতে যাওয়াকেও আমার পক্ষে দোষাবহ মনে হচ্ছে। যেখানে চল্লিশ বছর কাটিয়েছি, যেখানকার বাতাস আমার জীবন বাঁচিয়েছে, যে গ্রামের রূপ দেখে জ্যোৎস্নারাত্রে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছি এক একদিন, যেখানকার বাসিন্দাদের গলা জড়িয়ে ধরে পরস্পরের সুখে-দুঃখে হেসেছি, অশ্রু বিসর্জন করেছি, লজ্জার কথা, সেখানে আমি অনাত্মীয় আজ–নিজের মায়ের ওপর কোনো স্নেহের দাবিই নেই আমার, আইনের চোখে আমরা আজ বিদেশি! দেশে যেতে গেলেও চাই পাসপোর্ট, চাই ভিসা। এরকম লজ্জা বিশ্বের অন্য কোনো জাতি এত নিবিড় করে অনুভব করেনি বোধ হয়।
আজও নিয়মিতভাবেই আসে দুপুর, কিন্তু দেশের মতো ছুটে আমবাগানে গিয়ে দুপুরটা কাটাতে পারি না। গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহর আমাদের কাছে ছিল অত্যন্ত লোভনীয়–সকাল থেকে নুন-লঙ্কা গুঁড়িয়ে কাগজে জড়িয়ে রাখার ইতিবৃত্ত মনে করলে চোখটা সজল হয়ে ওঠে আজও। মা-বাবার তন্দ্রা আসার সঙ্গে সঙ্গেই সন্তর্পণে খিড়কি খুলে বাগানে পালানো বইপত্র ফেলে, তার তুলনা কোথায়! ছোটো বোনকে পরিবেশ-পরীক্ষক হিসেবে রেখে পালাতাম আমের লোভ দেখিয়ে-বেচারি ঠায় বসে থাকত গুরুজনদের মুখের দিকে তাকিয়ে, তাঁদের কারুর তন্দ্রা ভাঙবার আগেই সে ছুটে গিয়ে খবর দিত চুপিচুপি–আর আমিও ঠিক আগের মতোই আবার শান্তশিষ্ট ছেলের মতো অখন্ড মনোযোগ দিয়ে বিদ্যাভাসে লেগে যেতাম! বই খাতার নীচে থাকত আমের কুচি। নুন-লঙ্কা সহযোগে যথা সময়ে সেগুলোর সদব্যবহারও আমার পক্ষে ছিল একটা কর্তব্যকাজ! এই ধরনের ফাঁকি দেওয়া অবশ্য রোজ সমান চাতুর্যের সঙ্গে সম্ভব হত না। কোনো কোনো দিন বোনটির অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে রেখে যাওয়ার ফলে বিপদে পড়তে হত। সে দুষ্টুমি করে খবরই দিত না আর সেদিন। আমরা তো অকুতোভয়ে বৃক্ষ থেকে বৃক্ষান্তরে ফলাহারে উন্মত্ত হয়ে উঠতাম সময়ের দিকে না তাকিয়েই! অবসাদ এলে বা পেট ভরতি হয়ে গেলে গাছ থেকে নীচে নেমে দেখতাম সন্ধের আর বেশি দেরি নেই! সেদিন কপালে চড়-চাপড় যে পরিমাণ জুটত তার কথা আর নাই বা বললাম।
সন্ধেবেলায় ব্রাহ্মণপাড়ায় কাঁসর ঘণ্টা বাজাবার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গিয়ে হাজির হতাম প্রসাদ পাওয়ার লোভে। সেদিনের সে উৎসাহ-উদ্দীপনা আজ যদি কিছুটাও অবশিষ্ট থাকত তাহলে মনে হয় এতখানি মিইয়ে পড়তাম না দুঃখের ভারে। লাঞ্ছনা-অপমান পেয়ে পেয়ে মনের অপমৃত্যু ঘটেছে–সৌন্দর্যের মৃত্যু মানেই মানুষের মৃত্যু। যদি বাঁচতে হয় এগুলোকে আবার জাগিয়ে তোলা প্রয়োজন, কিন্তু যা প্রয়োজন এবং যা করা কর্তব্য তা সব সময় আমরা করি কোথায়? বাসস্থান, চাকুরিসংস্থান, দৈনন্দিন অনটনের ঘূর্ণির মধ্যে পড়ে কি আমাদের ভবিষ্যৎ তলিয়ে যাবে?
এ কি জীবন না জীবনের অভিনয়? এ প্রসঙ্গে হঠাৎ মনে পড়ে যায়, গ্রীষ্মকালে আমাদের থিয়েটার হত প্রতিবছর মহা ধুমধামের সঙ্গে। গ্রীষ্মবকাশের দিনগুলোকে স্মরণযোগ্য করার উদ্দেশ্যেই হত অভিনয়ের ব্যবস্থা। সচরাচর আমরা অভিনয় করতাম পৌরাণিক নাটক। নরমেধযজ্ঞ, বিল্বমঙ্গল, বনবীর, সগরযজ্ঞ, চন্দ্রগুপ্ত ইত্যাদির অভিনয় একদা মাতিয়ে তুলত সমগ্র গ্রামখানিকে। সবচেয়ে বড়ো কথা এই যে, এর মূল অভিনেতারা প্রায় সবাই ছিলেন গুরুজনস্থানীয়! বাবা, মামা, মেসো, পিসে, দাদা, ভাই সবাই মিলে পার্ট মুখস্থ করেছি সারা দিনরাত ধরে–একে ওকে হঠাৎ মাঝখান থেকে খানিকটা দরাজ গলায় অভিনয়াংশ শুনিয়ে দেওয়াটা অত্যন্ত মজার ব্যাপার ছিল। এতটুকু আবিলতা ছিল না তার মধ্যে। বাবাকেই হয়তো আমি অভিনয়ের ঘোরে এক ফাঁকে কখন বলে ফেলেছি–দেখো সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ। বাবা শুনে মুচকি হেসেছেন। তাঁর ছেলে রাতারাতি যে আলেকজাণ্ডার বনে গেছে সেটা বুঝতে কষ্ট হয়নি তাঁর। কিন্তু উজ্জ্বল সেই দিনগুলোর ওপর কালবৈশাখীর ঝড় এল কেন? মনের আনন্দে মিলে-মিশে কাজ করতাম, তার বিপক্ষে সুনিপুণ করে জাল পাতল কোন হৃদয়হীন ব্যাধ?
গ্রীষ্মের পরই শুরু হত বর্ষা। কাজলকালো মেঘমেদুর বর্ষা গ্রামটিকে থমথমে করে দিত একনিমেষে। টিপটিপ ইলশে গুঁড়ি থেকে ঝমঝম ধারার মুষলবৃষ্টি সবই লক্ষ করতাম সেই ছোটোবেলায় জানালায় বসে বসে। মাঠ-ঘাট জলে থই থই করত, কৃষকেরা ভিজতে ভিজতে কাজ করে আর গান ধরে মনের খুশিতে। শ্রাবণ দিনে চাষবাস আর রাত্রে মনসার পুথি পড়াই তাদের দৈনদিন কাজ। বানান করে করে অপটু পড়য়ার মতো পুথি পড়লেও তাতে আনন্দ পায় তারা বেশ–সেই সঙ্গে আনন্দ বিতরণও করে পড়শি ভক্তদের মনে। শ্রাবণ মাসের শেষদিনে লখিন্দর উপাখ্যান শেষ করে তারা পদ্মাপুরাণ জড়িয়ে উঠিয়ে রাখে চাঙে।
আজ মনে পড়ে কৃষ্ণকিশোর কীর্তনীয়াকে। বড় ভালো কীর্তন গান করত, সে ছিল গ্রামের প্রাণস্বরূপ। তার পালা-কীর্তনে মুগ্ধ হত না এমন লোক দেখিনি। সুললিত কণ্ঠস্বরে তাল-মান বজায় রেখে অকৃত্রিম ভক্তিভরে চোখ বুজে সে কীর্তন ধরত যখন,
ঘরে আছে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রবোধ দিব কেমনে
বুঝাইলেও বুঝ মানে না নিমাই চান্দ বিনে–
যেমন তৈলবিনে বাতি জ্বলে না,
প্রাণ বাঁচে না জল বিনে।
অথবা
শুয়েছে গো বিষ্ণুপ্রিয়া–
কালঘুমেতে অচেতন
মায়া-নিদ্রা তৈজে নিমাই হল সন্ন্যাসে গমন
আমি বিদায় হলাম, ওগো প্রিয়ে দেখে যাও
জনমের মতন।
তখন অতিবড়ো পাষন্ডেরও চোখে জল দেখেছি। কৃষ্ণকিশোরের গলা আজও মাঝে মাঝে ভেসে আসে বাতাসে, অনেক রাত্রে ধড়মড় করে উঠে বসি মনের ভুলে, কানে বাজে, সেই কৃষ্ণকিশোর যেন সতর্ক করার জন্যে গান ধরেছে—’বিদায় হলাম, ওগো প্রিয়ে দেখে যাও জনমের মতন!’ সত্যি বিদায় হয়েছি জন্মের মতো, কিন্তু সন্ন্যাস নিয়ে নয়, অপরাধীর চরম দন্ড দ্বীপান্তর গ্রহণ করে।
এই বিষাদময় দুঃখের মধ্যেও আনন্দের দিনগুলোকে বাদ দিতে মন সরে না। বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই থাকত আমাদের গ্রামে। শারদোৎসবই হত সবচেয়ে ধুমধামের সঙ্গে। মেঘমুক্ত আকাশ-বাড়ির প্রাঙ্গণে শিউলি ফুলের বন্যা, স্থলপদ্ম, জলপদ্মের সমারোহে মন থাকত এমনিতেই খুশি। মাঠে মাঠে ধানের শিশিরভেজা সোঁদা সোঁদা গন্ধে অনির্বচনীয় মনে হত আনন্দোচ্ছাসকে। শারদীয়ার আগের আর একটা দুষ্টুমির অনুষ্ঠানের কথাও বাদ দেওয়া চলে না। সেটা হল নষ্টচন্দ্র! ভাদ্রের শুক্লা চতুর্থীর রাত্রে এই নষ্টচন্দ্রের কোপে কত গৃহস্থ যে ব্যতিব্যস্ত হয়েছেন তার হিসেব নেই। রাত্রে কত যে চুরি গেছে গৃহস্থের মিষ্টি কুমড়ড়া, শসা, জাম্বুরা (বাতাবিলেবু) আর আখ তা ভুক্তভোগী গ্রামবাসীরা মনে মনে হয়তো একটা হিসেব করে নিতে পারবেন! একে চুরি বললে ভুল করা হবে। গাছের জিনিস ভাগ করে রেখে দেওয়া হত সকলের দরজাগোড়ায়। সকালে উঠে এসব দেখে কেউ বড়ো একটা আশ্চর্য হত না, শুধু যাদের বাগান থেকে ফল খোয়া গেছে তারাই পাড়ার দুষ্টু ছেলেদের উপলক্ষ করে সামান্য গালিগালাজ করত মনের দুঃখে! সে গালাগালও আজকের বাস্তব গালাগালের চেয়ে মিষ্টি ছিল ঢের। তার ভেতর খানিকটা স্নেহের আমেজও মেশানো থাকত, কেননা অনেকক্ষেত্রে বাড়ির দু-একটি ছেলেও যে সে চুরিতে যুক্ত থাকত।
আর একটা ভোজের মওকা জুটত ভাইফোঁটা উৎসবে। সে আর এক বিরাট ব্যাপার! গ্রাম সম্পর্কে বোন হলেও অনেকেই ফোঁটা দেবার অধিকারী। ফোঁটা নিতেই হবে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে। ফোঁটায় ফোঁটায় সেদিন কপালের অবস্থা হত সঙিন,–একইঞ্চি ‘লেয়ার’ পড়ে যেত পুরু কাজলের আর চন্দনের। বাড়ি ফিরতাম চন্দনচর্চিত বনমালীর ‘পোজে’-নড়তে চড়তেও বড়ো কষ্ট হত সারাক্ষণ ভালোমন্দ খেয়ে খেয়ে। বাঙালি ভাই-বোনের প্রীতি-বন্ধনের সে কী মধুময় স্মৃতি। ভাইয়ের দীর্ঘ-জীবন কামনায় বোনেদের কী সে আকুল আন্তরিকতা! ভাইদের কপালে কাজল-চন্দনের ফোঁটা দিতে দিতে বোনেরা ছড়া কেটে বলত,
প্রতিপদে দিয়া ফোঁটা,
দ্বিতীয়ায় দিয়া নিতা;
যমুনা দেয় যমেরে ফোঁটা
আমরা দেই আমাদের ভাইয়ের কপালে ফোঁটা।
আজ অবধি ভাইয়ের আমার যম দুয়ারে কাঁটা!
ঢাক বাজে ঢোল বাজে আরো বাজে কাড়া,
যাইয়ো না যাইয়ো না ভাইরে যমেরি পাড়া।
আজ অবধি ভাইয়ের আমার যম দুয়ারে কাঁটা!
পূর্ববাংলার ঢাকা জেলার প্রায় সর্বত্রই ভাইফোঁটার উৎসব চলত দু-দিন ধরে। প্রতিপদে দেওয়া হত ফোঁটা, আর দ্বিতীয়ায় বোনের দেওয়া প্রীতিভোজ। ভাইদের যমের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে যে বোনেরা আজন্ম এমনি করে প্রার্থনা জানিয়ে এসেছে বছর বছর, তাদের সেই অকৃত্রিম প্রীতির বিনিময়ে কী করেছি আমরা তাদের জন্যে? দুবৃত্তদের হাত থেকে বোনেদের মান-মর্যাদাটুকু পর্যন্ত রক্ষা করতে পারিনি! ভগিনীর সম্মান আমাদের প্রাণের চেয়েও যে অনেক বড়ো, একথা বিস্মৃত হয়েছিল আত্মবিস্মৃত বাঙালি। তাই তো আজকের এই লাঞ্ছনা!
এরপর থেকেই একনাগাড়ে চলল উৎসব। শীতে কড়কড়ে ভাত, সরপড়া ব্যাঞ্জন আর পিঠে-পায়েসের সমারোহ। পৌষ-সংক্রান্তি, মহা-বিষুব সংক্রান্তি। বাস্তু পুজোর ধুম। হাজার বছরের পূজিত বাস্তু আজ যে এমনিভাবে ত্যাগ করে আসতে হবে তা কে জানত? হায় বাস্তুদেব, অদৃষ্টের কী পরিহাস, তুমিও আমাদের রাখতে পারলে না! মাঘের প্রচন্ড শীতে অনূঢ়া মেয়ের দল সূর্যোদয়ের পূর্বে পুকুরে স্নান করে দুর্বাদল মুঠো করে ধরে আবাহন জানাত প্রাণের প্রতীক সূর্যদেবকে,
উঠো, উঠো সূর্যঠাকুর ঝিকিমিকি দিয়া…
উঠিতে না পারি হিমালয়ের লাগিয়া,
হিমালয়ের পঞ্চকন্যা সূর্যে করল বিয়া–
লও লও সূর্যঠাকুর লও ফুল পানি!…ইত্যাদি।
এই যে কৌমার্যব্রত, এই যে কৃচ্ছসাধন, এই কি তার সফল প্রতিদান? এখানেই শেষ নয়। এরপর চলত উদিত সূর্যের আরাধনা। গোময় প্রলেপিত আঙিনায় ইটের গুঁড়ো, বেলপাতার গুঁড়ো, চালের গুঁড়ো, আবির হলুদের গুঁড়ো, তুষের গুঁড়ো দিয়ে কত বিচিত্র চিত্রাঙ্কন হত বাড়ির উঠানে। মাসান্তে ব্ৰত সাঙ্গ হলে কুমারীরা গ্রামের বিশিষ্ট লোকেদের খাওয়াত নিমন্ত্রণ করে। এই মাঘমন্ডল ব্রত পুর্ববাংলার পল্লিজীবনের এক অচ্ছেদ্য অঙ্গ। এমনি ভুলে-যাওয়া ব্ৰত যে কত ছিল আমাদের গাঁয়ে তার ইয়ত্তা নেই।
গোটা চৈত্র মাসটা ঢাকের বাজনায় মুখরিত থাকত। গ্রামের সব যুবকরা আর প্রৌঢ়রা সন্ন্যাসী সেজে নামত গাজনে। কী কঠোর ছিল সেই ব্রহ্মচর্য! এতে কোনো জাতিভেদের বালাই থাকত না। উচ্চনীচ সবাই একসঙ্গে পূতচিত্তে গুরু-সন্ন্যাসীর অনুশাসন মেনে চলত। ঢাক-পাট নিয়ে তারা গান গাইত মহাখুশিতে–অনেক সময় নিজেরাই বাদক, নিজেরাই গায়ক। শেষের দিকে রাত্রে ‘কালীকাছ’ অনুষ্ঠানটি ছিল বড়ো মজার। কেউ একজন অবিকল মা কালীর সাজে সজ্জিত হয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরত বাজনার তালে তালে। সঙ্গে সঙ্গে চলত দলবল। ঘুমন্ত চোখে ছেলে-মেয়েরা জেগে উঠে সময় সময় ভয়ে শিউরে উঠেছে। চিৎকার করে নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছে মায়ের আঁচলের তলায়। শেষ দিন হরগৌরীর যুগল মূর্তি গৃহস্থের দুয়ারে দুয়ারে কল্যাণ কামনা করত। রাত্রে হত ব্রহ্মচর্যের কঠিন অগ্নিপরীক্ষা। নিজের চোখে দেখেছি দশ-বারো হাত দীর্ঘ জ্বলন্ত অগ্নিচুল্লির মধ্য দিয়ে সন্ন্যাসীরা অবলীলাক্রমে পার হয়ে চলে যেত। সুতীক্ষ খাঁড়ার ওপর উঠে নৃত্য করত হাসিমুখে!
পার্লামেন্ট সভ্যদের মধ্যে লজ্জাকর গালাগালি আর কাদা ছিটানো দেখে মনে পড়ে যায় আমাদের গ্রামের সেই বকুল গাছ-তলার কথা। ওইখানে জমত পার্লামেন্ট! আলোচনা, সমালোচনা, বিচার, বিধান প্রভৃতি সব কিছুরই নিষ্পত্তি হত বকুলতলায়। আমাদের গ্রামে কোনোকালেই পুলিশ আসেনি। এখানকার লোককে কোনোদিন আইন-আদালত কেউ দেখেনি করতে। তারা ছিল নিরীহ, শান্তিপ্রিয়, শাস্ত্রানুশীলনে রত। মেয়েরা ছিল ব্রত-পূজা পার্বণ নিয়ে ব্যস্ত। অশান্তি দেখিনি গ্রামের কোথাও।
আজ আমরা সবাই গ্রামছাড়া। বকুলতলায় বয়োবৃদ্ধদের মুখে শুনেছি, পূর্বে নদী ছিল এ অঞ্চলটায়। কালক্রমে চরা পড়ে পড়ে এবং মুসলমান আমলে ধীরে ধীরে বসতি হতে হতে গড়ে উঠল এই গ্রাম। আনোয়ার খাঁ বলে কে একজন প্রথম এই জায়গাটি আবাদ করে বলে তারই নাম অনুসারে নাকি গ্রামের নাম হয় আনোয়ারাবাদ বা আনরাবাদ। গ্রামের চতুষ্পর্শেই হিন্দু। একসঙ্গে এত হিন্দু খুব কম জায়গাতেই আছে। কিন্তু কালের গতি চিরকালই কুটিল। গ্রামের চারিদিক কানা বিল, ঘাগটিয়া বিল, গজারিয়া বিল, মহিষা বিল, দিলি বিল, রাজুখালি বিল ও ইনাম বিল দিয়ে ঘেরা। মনে হয় এই সপ্তবিল দিয়ে পরিবেষ্টিত করে প্রকৃতিদেবী শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্যেই আনরাবাদ তৈরি করেছিলেন। দুর্গের মতো চারধারে পরিখা অতিক্রম করে শত্রুর আক্রমণ সত্যিই ছিল এক অসাধ্য ব্যাপার। জানি না আবার আমরা পরিখা পেরিয়ে নিজের বাস্তুভিটেয় স্থান পাব কি না। আর কি কোনোদিন দুই বাংলা এক হয়ে আনন্দোৎসবে মাতবে না! কিপলিঙের ‘East is East and West is West কথাগুলোকে মিথ্যে প্রমাণিত করে আমরা কি জাতীয় বৈশিষ্ট্যের প্রমাণ কোনোদিন আর দিতে পারব না? হিন্দু-মুসলমান আবার আগের মতো নির্ভয়ে মনের সুখে পরস্পরের হাত ধরে বেড়াতে পারবে না, সে-কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না!
.
শুভাঢ্যা
সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া
দৈন্যের দায়ে বেচিব সে মায়ে এমনি লক্ষ্মীছাড়া!
দৈন্যের দায়ে বেচে আসিনি, প্রাণের মায়ায় ছেড়ে এসেছি আমরা আমাদের সোনার মাকে। কবিগুরুর লক্ষ্মীছাড়া তিরস্কার আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয় জানি, কিন্তু যে ব্যবস্থায় লক্ষ লক্ষ মানুষকে এমনি লক্ষ্মীছাড়া, গৃহহারা হতে হল সে ব্যবস্থার অধিকারীদের বিচারকর্তা কতকাল ঘুমিয়ে থাকবেন? এতগুলো অসহায় মানুষের আর্ত ক্রন্দনে বিশ্ব বিচারকের আসন কি টলে উঠবে না? যদি না ওঠে তাহলে তাঁর অস্তিত্ব নিয়েই যে প্রশ্ন। উঠবে!
কতটুকুই বা তার আয়তন। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে মাইলখানেক আর মাইল-দেড়েক মাত্র হবে হয়তো। কিন্তু দশ দশ হাজার লোকের ঘন বসতি ছিল একদা এ গ্রামে। ঢাকা শহরের দক্ষিণ তীরে বাবুর বাজার ও কালীগঞ্জ খেয়াঘাট থেকে শুরু করে একটা পথ জিঞ্জিরা গ্রামের গোরস্থানের পাশ দিয়ে এবং আর একটি পথ শুভাঢ্যা খাল ঘিরে তার পশ্চিম তীর দিয়ে শ্রীশ্রীগোপীনাথ জিউর আখড়ার নিকট এসে মিলিত হয়েছে। ঢাকা থেকে আসতে হলে এ আখড়া হয়েই আসতে হয় আমাদের গ্রামে। শুভাঢ্যা ছিল হিন্দুপ্রধান গ্রাম।
বাংলার এককালীন বিখ্যাত মল্লবীর স্বর্গত পরেশনাথ ঘোষের (ঢাকার পার্শ্বনাথ) জন্মভূমি, তাঁর শৈশব ও যৌবনের লীলাক্ষেত্র শুভাঢ্যা। এ গ্রাম ক্ষাত্রশক্তির জন্যে চিরকালই ছিল প্রসিদ্ধ। কিন্তু সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার কাছে সে ক্ষাত্রশক্তির পরাক্রম যে অতিসহজেই পরাভব মেনে নিল। এ পরাজয়ের কলঙ্ক আমাদের ভবিষ্যৎ পুরুষ কি মোচন করতে পারবে না কোনোদিন? না তারা শুধু অভিশাপই দেবে তাদের পূর্বপুরুষদের?
নামকরা শিক্ষাবিদ ডা. প্রসন্নকুমার রায় ও কলকাতার এককালের প্রসিদ্ধ ডাক্তার দ্বারকানাথ রায় এ গাঁয়েই হয়েছিলেন ভূমিষ্ঠ। তখনকার দিনে সমগ্র বিক্রমপুর ও নিকটবর্তী অঞ্চলের নৈয়ায়িক পন্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র সার্বভৌম এ গাঁয়েরই এক পর্ণকুটিরে বাস করতেন; টোলে সংস্কৃত শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন তাঁর ছাত্রদের। তাঁদের স্মৃতিপূত আমার পল্লিজননীকে চোখের জলে বিদায় দিয়ে এসে আমরা আজও বেঁচে আছি। কিন্তু এ বাঁচা যে মরার চেয়েও করুণ, তার চেয়েও বেদনাদায়ক।
কিন্তু চরম আঘাতে ভেঙে পড়লেও, চূড়ান্ত দুঃখের মধ্যে আজও সগৌরবে স্মরণ করি আমার গ্রামের নওজোয়ানদের আর তাদের অভিভাবকদের। বিদেশি চক্রান্তে বার বার ঢাকায় শুরু হয়েছে সাম্প্রদায়িক হানাহানি আর সেই উন্মত্ততা পার্শ্ববর্তী পল্লির শান্ত পরিবেশে করেছে অশান্তি উদগিরণ। আমার গাঁয়ের ওপরও তেমনি হামলা করার উদ্যোগ হয়েছে কয়েকবার। গোপীনাথ জিউর আখড়া অবধি এগিয়ে এসেছে উন্নত্ত জনতা–কিন্তু তার বেশি আর নয়। শুভাঢ্যার শুভবুদ্ধি তার সমগ্র সত্তা ও শক্তি নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে আর আক্রমণকারী দলের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা স্তিমিত হয়ে গেছে প্রতিবার সেই সম্মিলিত প্রতিরোধের সামনে।
সেদিনের কথা স্পষ্ট মনে পুড়ে। ‘৪৬ সাল। মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম’-এর তান্ডবলীলা চলছে কলকাতায়, ঢাকায়, প্রায় সারাবাংলা জুড়ে। বাইরে থেকে শুভাঢ্যার দিকেও এগিয়ে এল মারমুখো হয়ে একদল হাঙ্গামাকারী-সাম্প্রদায়িক ধ্বনি তাদের সুউচ্চ কণ্ঠে, সশস্ত্র তাদের বাহু। কিন্তু সুবিধা হল না। অল্প সময়ের মধ্যেই টের পেল তারা যে, এ বড়ো কঠিন ঠাঁই। দুর্জয় প্রতিরোধে স্তব্ধ হল সমস্ত কলরব, ব্যর্থ হল দূবৃত্তদলের অশুভ প্রবৃত্তি। শুভাঢ্যার জাগ্রত তারুণ্য সেবার শুধু তাদের আপন গ্রাম-জননীকেই রক্ষা করেনি, তাদের ঐক্যবোধ ও সাহসিকতায় রক্ষা পেয়েছে আশপাশের অন্যান্য পল্লিঅঞ্চলও। তবে তার জন্যে দক্ষিণাও বড়ো কম দিতে হয়নি শুভাঢ্যাকে। লিগ সরকারের পুলিশি গুলিতে প্রাণ দিতে হয়েছে আমার গাঁয়ের তিন তিনটি বীর জোয়ানকে। সেই গদাধর, ফুলচাঁদ আর ক্ষুদিরামের স্মৃতিতর্পণই কি করে চলেছি আমরা সব-হারানোর তপ্ত আঁখি-জলে? এ তর্পণের শেষ কি নেই?
আমার শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের লীলাক্ষেত্র, পিতৃপুরুষের ভিটে ও অতিআদরের জন্মভূমি সেই শুভাঢ্যা গ্রামটি ছিল কত বিচিত্র! গোপীনাথ জিউর আখড়া থেকে শুরু করে যে দো-পায়া সড়কটা অনেকটা খাল ও নালা ডিঙিয়ে গাঁয়ের একেবারে শেষপ্রান্তে এসে পৌঁছেছে, তারই একটি শাখা আবার গাঁয়ের পশ্চিমাঞ্চল বেয়ে আঁকাবাঁকাভাবে পশ্চিমপাড়ার খেলার মাঠে মূল সড়কটার সঙ্গে এসে মিশেছে। উত্তরপাড়া, পূর্বপাড়া ও পশ্চিমপাড়ায় বিভক্ত ছিল আমাদের গ্রামটি। তার প্রত্যেকটি পাড়া ছিল আবার নির্দিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের পেশা অনুসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অঞ্চলে ভাগ করা। যেমন কামারহাটি, মাঝিহাটি, বৈদিকহাটি ইত্যাদি। পুজো-পার্বণ, খেলাধুলো, গান-বাজনা প্রভৃতি প্রত্যেক অনুষ্ঠান নিয়ে এ তিন পাড়ায় কত হইচই প্রতিদ্বন্দ্বিতাই না ছিল! পশ্চিমপাড়ার জনবল ও অর্থবল বরাবরই ছিল বেশি। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাকি দু-পাড়াকে হার মানিয়ে দিত তারা। উত্তরপাড়ার জনবল ছিল কম। তাই ওপাড়ার ছেলের দল খেলাধুলো ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিত পশ্চিমপাড়ার সঙ্গেই।
পদ্মা পার হয়ে চলে আসতে হয়েছে। কিন্তু ছেড়ে আসা গ্রামের সেই পুরোনো স্মৃতি কি বিস্মৃত হওয়া যায়? পুজোর দিন ঘনিয়ে আসতেই আমাদের মতো প্রবাসীদের মধ্যে দেশে যাবার কী ধুমই না পড়ে যেত। কাপড়চোপড়, অন্যান্য দরকারি জিনিসপত্র গোছগাছ করে অনেকদিন আগে থেকেই আফিস ছুটির প্রতীক্ষায় দিন গুনতাম। আর দেশে যাবার দিনটিতে গাঁয়ে ফেরার মহানন্দে ঢাকা মেলে সে কী ভিড়! জোর ঠেলাঠেলি–সবাই উঠতে চায় গাড়িতে একসঙ্গে–তর সয় না কারুর। দাঁড়িয়ে তল্পা নিয়ে সবাই চলেছে দেশের বাড়িতে বাদুড়ঝোলা হয়ে। ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে যে কতবার গোয়ালন্দ পর্যন্ত চলে গেছি, তার ঠিক নেই। মনের আনন্দে কখন যে সুর ভাঁজতে শুরু করে দিয়েছি ট্রেন চলার তালে তালে তা নিজেরই হয়তো খেয়াল নেই। কখনো হয়তো বা জেনেশুনে মতলব করেই গেয়ে ফেলেছি,
ফিরে চল, ফিরে চল, ফিরে চল
আপন ঘরে।
আমার গানে দোলা লেগেছে আর-সব ঘরমুখো যাত্রীদের মনে। কিন্তু আজ পরমুখো হয়ে যেভাবে ঘুরে মরছি আমরা দোরে দোরে তার অবসান কবে ঘটবে, কবে ফিরে পাব আমরা আমাদের জীবনের সেই হারানো সুরকে! আমাদের মতো প্রকান্ড একটা গ্রামের আট-দশখানা দুর্গা পুজোর মধ্যে কেবলমাত্র দু-খানা ছিল সর্বজনীন। ব্যক্তিগত পুজো অপেক্ষা এ দুটি পুজোই হত খুব ঘটা করে ও হইহুল্লোড়ের মধ্যে। ঢাকিদের ঢাক বাজনায় সারাগ্রাম মুখরিত হয়ে উঠত। দশহরার দিন বড়ো বড়ো পেটওয়ালা পাটের নৌকো ভাড়া করে প্রতিমা ভাসান হত। নৌকোগুলোকে নানাস্থান ঘুরিয়ে রাত্রিবেলা বুড়িগঙ্গার অপর পার–ঢাকা শহরের ‘বাকল্যাণ্ড বাঁধে’ ভিড়ানো হত। বিরাট এক মেলা বসত সেখানে এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই আসত প্রতিমা দর্শন করতে। মিঠাই-মন্ডা খেয়ে সারারাত জেগে প্রতিমা নিরঞ্জনের পর সবাই বাড়ি ফিরত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে।
মনে পড়ে আমাদের পশ্চিমপাড়ার খেলার মাঠের কথা। পাঠ্যাবস্থায় গ্রীষ্মের লম্বা ছুটিতে ওইটুকুন চতুর্ভুজ মাঠে ফুটবল খেলার কী বিরাট ধুমই না পড়ে যেত! ওই মাঠেই অনুশীলন করে আমরা আশপাশের–এমনকী বিক্রমপুরস্থ দূর গ্রাম থেকেও কত শিল্ড-কাপ জয় করে নিয়ে এসেছি তার ঠিক নেই।
ছেড়ে-আসা গ্রামের আরও অনেক কিছুই আজ মনে পড়ে। মনে পড়ে, শীতের সময় শিবরাত্রির উৎসবের কথা। রাত্রি জাগরণের নামে সবাই যখন নির্জলা উপবাসে কাতর, আমরা তখন গাঁয়ের গৌর মুদি, আদিত্য ভট্ট আর শরৎ ভট্টদের খেজুর গাছের রস চুরি করে। খেতাম। শীতে ঠকঠক করে কাঁপত সবার শরীর। কিন্তু তাতে কী?
চৈত্র মাসে চড়ক পুজোর কথাও ভুলতে পারা যায় না। গাজন দলের লোকেরা বাড়ি বাড়ি কত সং দেখিয়ে বেড়াত, বেদে-বেদেনির নাচ নাচত। গাঁয়ের কবিয়ালরা চমৎকার নতুন নতুন গান বেঁধে তাদের সহায়তা করতেন। কুমাই মুদি আর ট্যানা সাধু প্রভৃতি সেসব জনপ্রিয় কবিয়ালরা আজ কোথায়?
আমি তখন একেবারেই ছোটো। পাঠশালার নীচের ক্লাসে পড়ি। আমাদের গাঁয়েরই এক বাড়িতে কবিগানের আসর বসেছে। আমিও তার একজন উৎসুক শ্রোতা। ওইটুকু বয়সে সে গানের অর্থ বোঝা দুরূহই ছিল আমার পক্ষে। তবু দু-পক্ষের কবির লড়াই যে খুবই উপভোগ করেছিলাম, সে-কথা আজও বেশ মনে পড়ছে। কী অস্বাভাবিক কবিত্বশক্তি দেখেছি সেকালের কবিয়ালদের। সঙ্গে সঙ্গে কবিতায় উত্তর-প্রত্যুত্তর চলেছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। কখনো চলেছে কেচ্ছা এবং পাল্টা কেচ্ছার তুফান আবার কখনো বা চলেছে ধর্মালোচনা। তার প্রায় সবটাই ছিল আমার উপলব্ধির বাইরে। তবু নেহাত হজুগে মেতে এবং কবিয়ালদের অদ্ভুত কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হয়ে সারারাত কাটিয়ে দিয়েছি কবিগান শুনে। বড়ো হয়েও কবিগান শুনেছি নতুন নতুন দলের। সেসব গান বুঝেছি, তার অন্তর্নিহিত কথা উপলব্ধি করেছি। সখী-সংবাদের একটি গানের কয়েকটি পদ এখনও ভুলতে পারিনি। শ্যামের আগমন প্রতীক্ষায় সেজেগুজে প্রায় সারারাতই কাটিয়ে দিলেন বিনোদিনী রাধা। কৃষ্ণ যখন এলেন শ্ৰীমতীর কুঞ্জদ্বারে তখনকার পরিবেশ এবং তার প্রতিক্রিয়া কী নিখুঁতভাবেই না বর্ণনা করেছেন পুববাংলার কবিয়াল! দুই দলের বাদ-প্রতিবাদ ও হাস্যপরিহাস চলেছে অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু যখনি আরম্ভ হয়েছে তত্ত্বকথা বা অবতরণ করা হয়েছে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের, তখনই সমগ্র জনতা হয়ে গেছে একবারে নীরব নিথর। কবি গেয়েছেন,
শ্যাম আসার আশা পেয়ে, সখিগণ সঙ্গে নিয়ে বিনোদিনী
যেমন চাতকিনী পিপাসায়, তৃষিতা জল আশায়
কুঞ্জ সাজায় তেমনি কমলিনী।।
সাজাল রাই ফুলের বাসর, আসবে বলে রসিক নাগর,
আশাতে হয় যামিনী ভোর, হিতে হল বিপরীত।
ফুলের শয্যা সব বিফল হল, অসময়ে চিকণ কালা এল–
রঙ্গদেবী তায় ধারণ করে দ্বারে গিয়ে।
এর পরেই সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে ধুয়া,
ফিরে যাও হে নাগর, প্যারী বিচ্ছেদে হয়ে কাতর
আছে ঘুমাইয়ে।
ফিরে যাও শ্যাম তোমার সম্মান নিয়ে।
এমনি ভাষায় কৃষ্ণকে সতর্ক করে দিয়েই ক্ষান্ত হননি কবি। তিনি মুখের ওপর শ্যামকে আরও কড়া কথা শুনিয়ে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, তাঁকে তরুণী হত্যার দায়ে ফেলারও ভয় দেখিয়েছেন তিনি, বলেছেন শ্যামসুন্দরকে,
ছিলে কাল নিশীথে যার বাসরে।
বঁধু তারে কেন নিরাশ করে, নিশি শেষে এলে রসময়!
বঁধু প্রেমের অমন ধর্ম নয়।
তুমি জানতে পারো সব প্রত্যক্ষে, দুই প্রেমেতে যেজন দীক্ষে
এক নিশিতে প্রেমের পক্ষে, দুই-এর মন কি রক্ষা হয়।
প্যারী ভাগের প্রেম করবে না, রাগেতে প্রাণ রাখবে না,
এখন মরতে চায় যমুনায় প্রবেশিয়ে।
চাঁদোয়ার নীচে গাঁয়ের মাটিতে বসে এমনি সব কবিগান আর হয়তো শোনবার সুযোগ হবে না কোনোদিন!
‘চৈত্র-সংক্রান্তি’র আগের দিন হরগৌরী নৃত্য ও তার সঙ্গে নানাপ্রকার নাচগান হত। যখন ছোটো ছিলাম, স্কুলে পড়তাম–ওদের মতো আমরাও সং সেজে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়াতাম –পয়সা সংগ্রহ করতাম। আর তার সদ্ব্যবহার করতাম চড়ক-পুজোর মেলায়। এ উপলক্ষে ‘চন্দ্রপিকারা’র মেলা কত নামকরাই না ছিল–দূর দূর গ্রাম থেকে কত লোকই না আসত এ মেলায়!
প্রখর গ্রীষ্মের ভীষণতা অসহ্য মনে হত। কিন্তু বর্ষাকালে আমাদের গাঁয়ের চেহারাই যেত পালটে। সমস্ত মাঠ, ঘাট, খেত-খামার জলে থই থই করতে থাকে বর্ষায়। দূর গাঁয়ের জলে ঘেরা পাড়গুলোকে ছোটো ছোটো দ্বীপ বলে ভুল হত। পায়ে-চলা পথ প্রায় সবটাই হয়ে যেত অদৃশ্য। নৌকোই তখন যাতায়াতের একমাত্র বাহন। ধান আর পাটগাছের সবুজ মাথার ওপর দিয়ে যখন মেঠো হাওয়া হুহু করে বয়ে যেত, সান্ধ্য পরিবেশে কী মনোরমই না লাগত সে দৃশ্য! বিকেলে নৌকো করে রোজ বেড়াতে যেতাম আমরা সে পরিবেশ, সে দৃশ্য উপভোগ করতে।
মনসা ভাসান উপলক্ষে শুভাঢ্যা খালের একপ্রান্তে হরির মঠ-সংলগ্ন বিরাট জলাভূমিতে ‘নৌকোবাইচ’ হত ও মেলা বসত। ছোটো-বড়ো সব ধরনের নৌকোই এ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করত সুসজ্জিত হয়ে। মাঝি ও দাঁড়িরা তালে তালে বৈঠা ফেলত লোকসংগীতের ঝড় বইত সঙ্গে সঙ্গে। নৌকোয় নৌকোয় ভাসমান মেলাই যেন এক-একটি বসে যেত। তাদের কোনোটাতে থাকত নানা পণ্যসম্ভার, কোনোটাতে ক্রেতা, কোনোটাতে বা দর্শক।
কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসের দিকে জলে যখন টান ধরত, তখনকার প্রধান আকর্ষণ ছিল মাছ ধরা। জল কমে আসায় তখন পুকুর, ডোবা, নালায় এসে আশ্রয় নিত মাঠের মাছগুলো। ছিপ, পলুই বা জাল ফেলে মাছ ধরার তখন মহাধুম পড়ে যেত চারদিকে। জীবন্ত পুঁটি ‘খোটে, খোটে উঠত বঁড়শিতে। বড়ো বড়ো শোল আর গজাল মাছ ধরারই বা কী আনন্দ! টোপ গেলার সঙ্গে সঙ্গেই দৌড়ে গিয়ে ছিপ টেনে মাছ তুলতে সে কী ছুটোছুটি! একটু দেরি হলে শিকার হাতছাড়া হবার খুবই সম্ভাবনা। মৎস্য ধরিব খাইব সুখে’–কথাটা পূর্ববাংলার এই নীচু জলাভূমির ক্ষেত্রেই বুঝি বেশি খাটে!
আমাদের ছেড়ে-আসা গ্রামের এমনি কত কথা–এমনি কত স্মৃতি আজ চোখের সামনে এসে ভিড় করে–মানসপটে দেখা দেয় পল্লিমায়ের এমনি কত স্নেহসিক্ত রূপ। জীবনের এতগুলো বছর যার স্নেহক্রোড়ে কেটে গেছে হাসি-কান্না রং-তামাশার মধ্য দিয়ে, তার কোলে ফিরে যেতে আবার যে সাধ যায়–ইচ্ছে হয় পরমপীঠস্থান আমার জন্মভূমিকে আবার আপনার করে ফিরে পেতে!
.
নটাখোলা
রাজনীতি কীর্তিনাশা পদ্মার ওপরেও টেক্কা দিয়েছে বিংশ শতাব্দীর মাঝখানে এসে! পদ্মা এক পাড় ভেঙে অন্য পাড়ে সমৃদ্ধির প্রাসাদ তোলে, কিন্তু ভেজাল রাজনীতি বড়ো নির্মম! পিতৃভূমি ত্যাগ করে আজ কত নিরাশ্রয় মানুষ দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাপাত্র সম্বল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের দুঃখ কোথায় গিয়ে ঠেকেছে তার উপলব্ধি অধিকাংশ মানুষের মনকে স্পর্শও করছে না! সমস্ত জীবন সুখে কাটিয়ে শেষজীবনে যাঁরা দুটি ভাত-কাপড় আর একটুখানি নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে হন্যে হয়ে মানসম্মান হারিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাঁদের অবস্থার কথা ক-জন ভাবছেন দরদ দিয়ে? স্বাধীনতার জন্যে জীবন বিপন্ন করেছি আমাদের ভয়ে একদিন বিদেশি শক্তিও ভীত হয়েছিল, কিন্তু ভ্রাতৃবিরোধ সেই ঐতিহ্যটুকু হরণ করে সর্বদিক থেকে যেন সমস্ত বাঙালি জাতিকে হীন করে তুলেছে। বাংলার মানুষ আত্মীয়বোধে জীবন দিতে পারে, কিন্তু আজ হীন স্বার্থ বড়ো হয়ে উঠে মানুষের মানবতাবোধকেও যেন বিপর্যস্ত করতে বসেছে। আমাদের এই যে অপমৃত্যু এর জন্যে দায়ী কে? জাতীয় ঐতিহ্য বিসর্জন দেওয়া আর আত্মহত্যা করা দুই-ই যে সমান কথা।
পদ্মার কুলুকুলু ধ্বনি একদিন মনে যে আমেজ আনত আজ আর গঙ্গার কূলে বসে সে অনুভূতি যেন পাই নে। আমাদের অবস্থা যেন সেই ছড়া-বর্ণিত এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর’ গোছের। দুঃখ-লাঞ্ছনা ভোগ করে করে অবস্থা হয়েছে স্যাণ্ডউইচের মতো নিষ্পিষ্ট। গ্রামের মানুষ আমরা, শহরজীবনে অভ্যস্ত নই। তাই পদে পদে কলকাতায় পায়রা খুপি অস্বাস্থ্যকর ঘর নামধেয় বস্তিজীবন আমাদের শ্বাসরোধ করে তুলছে দিন দিন। এই দ্বীপান্তর থেকে কবে মুক্তি পাব তা ঈশ্বরই জানেন। ছেড়ে-আসা গ্রামকে আজ তাই বেশি করে মনে পড়ছে। খুঁটিনাটি জীবনকথা চোখের সামনে ভেসে উঠে মনকে উদাস করে তুলছে। বার বার। মুক্ত জীবন, মুক্ত বাতাস একে উপড়ে নিয়ে এই যে ইটকাঠ-ঘেরা কারাগারে আমাদের জোর করে বন্দি করে রাখা হয়েছে একে কি স্বাধীনতা আখ্যা দিয়ে সম্মানিত করা মৃতপ্রায় মানুষের পক্ষে সম্ভব?
পদ্মার উত্তাল তরঙ্গ কূল ছাপিয়ে তীরবর্তীদের ভিজিয়ে দিত, আর সেই ঢেউয়ের বুকে দুলে দুলে চলত গাঁয়ের কতরকমের নৌকো। কোনো কোনোটার বুকে আঁকা থাকত ছোটো ছোটো লাল তারকা। গাঁয়ের ছেলেরা ঝাঁকে ঝাঁকে বাঁকে বাঁকে, ডিঙি নৌকোয় মাছ ধরত; কৈবৰ্তরা ঘাটে ঘাটে তাদের ডিঙি ভিড়িয়ে সেই মাছ কিনে নিত। গ্রাম ছেড়ে সে মাছ চলে যেত দূরে–কত দূরে–কলকাতায়। সকাল থেকে সন্ধে নাগাদ পদ্মার বুকে চলত হাজার হাজার নৌকোর আনাগোনা–দেশি, বিদেশি ছোটো ছোটো ডিঙির মাঝখান দিয়ে পাল তুলে চলত বড়ো বড়ো হাজারমনি পাঁচ-শোমনি চালানি নৌকো–দূর থেকে মনে হত ছোটো ছোটো পাতিহাঁসের দলে চলেছে যেন এক-একটা বড়ো বড়ো রাজহংস।
নারায়ণগঞ্জ লাইনের স্টিমারগুলো গোয়ালন্দ বন্দর থেকে ছেড়ে এসে মাঝখানটায় কাঞ্চনপুরে ভিড়ত; সেখান থেকে স্টিমার ছাড়বার ভোঁ পদ্মার বাতাসে ভেসে ভেসে এসে পড়ত আমাদের স্টেশনঘাটে। সে ধ্বনি ইলামোরার মাঠ পেরিয়ে আইড়মাড়া বিলের ওপারেও শোনা যেত ভিন গাঁয়ে। পাটগ্রাম, পাঠানকান্দি, হেমরাজপুর, বাহাদুরপুর–এ পরগনার প্রায় সমস্ত লোকই জানত–শহর কলকাতা থেকে তাদের প্রবাসী কুটুম্ব ওই স্টিমারে আসছে। ভোরের সেই স্টিমারের ভোঁ, আর সন্ধ্যার গোয়ালন্দগামী স্টিমারের বাঁশি এ গাঁয়ের এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের নর-নারীর মনে জাগিয়ে তুলত মিলনের আনন্দ, বিচ্ছেদের বেদনা। আজও সকাল-সন্ধ্যায় শোনা যায় সেই স্টিমারের ভোঁ। কিন্তু স্টিমারঘাটে নেই সে ভিড়–নেই আর সেই দোকানপাট। ছেলেরা পালিয়েছে, নয়তো মরেছে না খেয়ে–কৈবৰ্তরা পালিয়ে এসেছে রাণাঘাটে, নয়তো নবদ্বীপে। এখন কি সেই বিরাট চালানি নৌকো তেমনি পাল তুলে চলে? বড়ো বড়ো পানসিগুলো নদীপারের যাত্রী নিয়ে আজ কি পদ্মার বুকে পাড়ি জমায়? ঘাটে ঘাটে গাঁয়ের মেয়েদের কচকচানি, ছেলে-মেয়েদের জলে দাপাদাপি হয়তো ফুরিয়ে গেছে, শাঁখ বাজিয়ে ঘণ্টা পিটিয়ে গঙ্গাপুজোরও হয়ে গেছে হয়তো অবসান!
ছত্রিশ জাতের গ্রাম ছিল আমাদের নটাখোলা। ব্রাহ্মণপাড়ার ভট্টাচার্যদের বাড়িতে বাড়িতে ন্যায়ালংকার, বিদ্যালংকার, তর্কতীর্থ, তর্কতীর্থ, কাব্যতীর্থদের টোলে ঢুকে ঢুকে দেখেছি, টোলের প্রবাসী ছাত্ররা সুর করে পড়ত বেদ-বেদান্ত, স্মৃতি, তর্কশাস্ত্র, কাব্য, দর্শন। গোঁসাইপাড়ার গোস্বামীগণ শোনাতেন চৈতন্যচরিতামৃত। আধুনিক গাঁয়ের একমাত্র মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়ের ছেলেরা ইংরেজির দুরূহ উচ্চারণ অভ্যাস করত চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করে। তাদের বিজাতীয় বিকৃত উচ্চারণে চমকে চেয়ে থাকত কলসি কাঁখে পদ্মার ঘাটে গমনরতা গাঁয়ের কুললক্ষ্মীরা। গাঁয়ের হাঁটা-পথে ধাবমান বলদজোড়াকে আপন মনে যেতে দিয়ে লাঙল কাঁধে করিমচাচা অথবা মহেন্দ্র বিশ্বাস সেই পড়য়াদের ইংরেজি বুলিতে হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ত–ওরা হয়তো মনে করত গুহ, বসু ও মজুমদার বাবুদের ছেলেরা তাদের গালাগাল দিচ্ছে। সেই ব্রাহ্মণপাড়ার কোল ঘেঁষেই মস্তবড়ো দাসপাড়া। এ পাড়ায় থাকত গাবর দাসেরা। এদের কাজ ছিল সম্পন্ন গৃহস্থবাড়ির কাজ করা–ভিটেয় মাটি তোলা, বাগান তৈরি করা, ধান মাড়াই করা ও ফাইফরমাশ খাটা। এতেই সুখে-দুঃখে পঞ্চাশ-ষাট ঘর দাসেদের চলত অনাবিল জীবনপ্রবাহ।
দাসেদের পাড়া পেরিয়ে গেলেই সাহাদের বাড়িঘর। এরা সবাই ছিল সম্পন্ন, যেমন শ্রী ছিল ঘরদোরের তেমনি ফুটফুটে আঙিনা। তাঁদের অনেকেই করত চালানি কারবার। সেই চালানির পেঁয়াজ, রসুন, তিল, সরষে, খেজুর গুড়, কলাই ছাঁদি-নৌকোয় ভরে গাঁয়ের মাঝিমাল্লারা ‘গাজি পাঁচপীর বদর বদর’ বলে পদ্মার বুকে ভাসিয়ে দিত সপ্তডিঙা মধুকর। এমন পাকা মাঝি ছিল তারা যে, কোনোদিন নৌকো ডুবে যায়নি তাদের, যদিও তারা সুন্দরবন পেরিয়ে এসেছে কলকাতায়, উজান ঠেলে গিয়েছে আসামের ধুবড়ি, তেজপুরে। কলকাতার পর ওরা গিয়েছে পাটনায়, কানপুরে-ফিরে এসেছে সরষের তেল নিয়ে, বিহারি আখিগুড়ে নৌকো ভরতি করে। আর আসাম থেকে ওরা এনেছে ধান আর ধান-কত ধান! এই গাঁয়ের ঘাট থেকেই রপ্তানি হত ঝিটকা বন্দরের প্রসিদ্ধ হাজারি গুড়, কিন্তু পরিমাণ ছিল বড়ো অল্প। আজকালকার ফিটকারি মেশানো নকল হাজারি গুড় সে নয়। আসল হাজারি গুড় বেশি সাদা হয় না–তাতে পায়েস রান্না করলে দুধও জমে যায় না। কাঁচা রসের সুমিষ্ট গন্ধে পদ্মার ঘাট মিষ্টি হয়ে যেত মাত্র দু-এক মন হাজারি গুড়ের সুগন্ধে। কোথায় লাগে তার কাছে। ভীম নাগের সন্দেশ-কলকাতার নলেন গুড়! যা খেয়েছি আজও যে তার আস্বাদ ভুলে যেতে পারছি না। হাজারি শেখ জন্মেছিল ক-পুরুষ আগে জানি না, হাজারি নিজে কিন্তু ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমায় অমর হয়ে রয়েছে–থাকবেও।
সাহাপাড়ার ডান পাশেই পুবের দিকে আইড়মারার মাঠের কোল ঘেঁষে উত্তর-দক্ষিণে ছিল তাঁতিপাড়া-মুসলমান কারিগর। মাঝখানটায় একটা মাত্র গেঁয়োপথের ব্যবধান–হিন্দু মুসলমানের সীমান্তরেখা। দিবারাত্র শুনতাম খটাখট শব্দ। তাদের মাকু চালানোর আওয়াজ আইড়মারার বিল পেরিয়ে, পাঠানকান্দির গ্রাম ছাড়িয়ে শোনা যেত ইছামতী নদীর কোলের বন্দরে–লেছড়াগঞ্জে। বন্দরের ব্যাবসায়ীরা সেই তাঁতিদের কাপড়, শাড়ি, চাদর, গামছা বিকিয়ে দিত ঘরে ঘরে। পঞ্চাশের মন্বন্তর এল–সেই তাঁতিকুল সুতোর অভাবে বেকার হয়ে গেল, না খেয়ে শুকিয়ে মরল অনেকে। দুর্ভিক্ষের পরে এল মহামারি! গ্রাম উজাড় হয়ে যায়! আমি নিজে ধরনা দিলুম তৎকালীন চিকিৎসামন্ত্রীর কাছে–ফল হল না কিছু। সামান্য কজন কর্মী যতটা পারি করলাম। স্বাভাবিকভাবেই মরে মরে ফুরিয়ে এল সেই মহামারি। তাঁতিপাড়ার আওয়াজ তখনও বন্ধ হয়নি। দেশ ভাগ হবার পূর্ব পর্যন্ত চলেছে কোনোক্রমে। তারপরে ধীরে ধীরে থেমে গেছে–সাতাশ ঘরের সাতঘর হয়তো টিকে আছে। তাঁত বেচে ফেলেছে–খেতখামারে নিড়ানি দিয়েছে তারা–নিড়ানো ফুরিয়ে গেছে, এখন তারা নিকটের শহরের পথে পথে হেঁটে বেড়ায়,–পাকিস্তানি কোঁদল শোনে–আর ভাবে, এ জীবনের আর কত বাকি!
চাষিরা ছিল দু-জাতের। হিন্দুও ছিল, তবে মুসলমানই বেশি। তারা নির্দিষ্ট কোনো পাড়ায় থাকত না। যেকোনো দিকে হিন্দু-মুসলমানের ঘর পাশাপাশিই ছিল। ব্রাহ্মণ হলেও, আমাদের বাড়িটার ঠিক গা ঘেঁষে তিনদিকেই ছিল মুসলমান প্রতিবেশী–সবাই চাষি। জহিরুদ্দিন শেখের স্ত্রী আমাদের ছিলেন বড়োচাচি, বুধাই শেখের সুন্দরী স্ত্রীকে বলতাম ‘ধলা-ভাবি’ গোপাল শেখের স্ত্রীকে তো ভাবি বলেই ডাকতাম–কারণ গোপাল আমার বাবাকে ‘বাবা’ই বলত। আমার বাবা ডা. হৃদয় ভট্টাচার্যকে সারাপরগনার লোকেই চিনত। ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের প্রথম পর্যায়ের পাশ করা ছাত্র ছিলেন তিনি, পাশ করা হৃদয় ডাক্তার। গোপাল একবার কলেরায় আক্রান্ত হয়ে তাঁর চিকিৎসায় বেঁচে উঠে পিতৃদেবকে বাবা বলে ডেকে চিকিৎসার দক্ষিণা দেয়–সেই থেকে চিরদিনই ছিল সে আমাদের বড়ো ভাই। আমাদের সুখের দিনে বাবরি চুল ঝুলিয়ে লাঠি নিয়ে নাচত আর দুঃখের দিনে–শোকে-সন্তাপে আমাদের উঠোনে গড়াগড়ি দিয়ে সবার সঙ্গে সমানে কাঁদত। ধমক খেয়ে বাগানের আমগাছ কেটে শ্মশানযাত্রার ব্যবস্থাও করে দিত। মোল্লাপাড়ার মাজুদিদিকে আজও পারি না ভুলতে। আমার মাকে তিনিও মা বলেই ডাকতেন। রাত্রির আঁধারে বোরখা পরে, চাকরের হাতে লণ্ঠন দিয়ে চটিজুতো পায়ে তিনি সপ্তাহে প্রায়ই আসতেন আমাদের বাড়ি-তখনকার দিনে মেয়েদের জুতো পরার রেওয়াজ হয়নি। কাজেই মাজুদিদির ওই অপরূপ মূর্তিটা চোখে বেশি করেই বাজত। দিদির কাজ ছিল ভারি মজার। যত রাজ্যের ভালো ভালো জিনিস চাকরকে দিয়ে বয়ে নিয়ে এসে আমাদের সকল ভাইবোনকে, মা, দিদিকে সামনে বসে খাইয়ে তবে তিনি যেতেন। কোনো নতুন জিনিস তাঁর আগে আমাদের কেউ এনে দিতে পারত না। দিদি ছিলেন নিঃসন্তান–আমাদের কোলে না নিতে পারলে তাঁর ভালো লাগত না। কতদিন পন্ডিত মশাইয়ের মার খাবার ভয়ে পালিয়ে গেছি মাজুদিদির বাড়িতে সেই পতিত জমির ওপারে। মাজুদিদির কোলে বসে কতদিন মজা করে দুধ-ভাত খেয়েছি। মর্তমান কলা দিয়ে আর পুরোনো খেজুরগুড় মিশিয়ে। আমার ব্রাহ্মণত্ব তাতে ঘোচেনি। মা জানতেন, বাবা তো ছিলেন সাহেব। নিষেধের প্রাচীর সেই পুরোনো দিনে আমাদের ভ্রাতা-ভগ্নীর সম্বন্ধটাকে ঘিরে ফেলতে পারেনি। এর সঙ্গেই মনে পড়ে সেই ছোটোবেলার শীতের দিনের কথা। গাছের তলায় সকালের রোদ্দুরটা আগে এসে পড়ত আমাদের বাড়িতে। সেইখানটায় ছেঁড়া চট বিছিয়ে ইস্কুলের পড়া তৈরি করতুম। এক এক ফাঁকে ক্ষেপু শেখের স্ত্রী ‘চাচি’ হাতছানি দিয়ে ডাকতেন। ছুটে গিয়ে কাঁটাল পাতায় করে সদ্য তৈরি নতুন গুড়ের ‘চাঁচি’ নিয়ে মহাআনন্দে রোজ চাখতুম। পঞ্চাশের ধাক্কায়ও বেঁচে ছিলেন চাচি, যদিও তাঁর তিনকুলে কেউ ছিল না। কিন্তু যেই আমরা দেশ ছেড়েছি চাচি আর বেঁচে থাকতে চাইলেন না। শুনেছি তাঁকে পদ্মার ভাঙাপারের ফাটলে ফেলে দিয়ে মাটি চাপা দিয়েছে গাঁয়ের দয়ালু মুসলমানেরা, ছাফন কাফনের খরচা জোটেনি। এই কলকাতায় বসে যতদিন ভেবেছি ছুটে গিয়ে চাচির সেই কবরখানা দেখে আসি, আর ফেলে আসি সেখানে তাঁর দেশছাড়া এক জিম্মি-ছেলের কয়েক ফোঁটা অশ্রু। রাক্ষুসি পদ্মা কি সে কবর এখনও রেখেছে?
গ্রামের একটাই ছিল প্রধান রাস্তা–প্রথমে লোকাল বোর্ডের, পরে উন্নীত হল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কে। পদ্মাপার হতে মহকুমার সদর মানিকগঞ্জ পর্যন্ত ষোলো মাইল রাস্তা। সেই পথের পাশ ধরেই থাকত কৈবৰ্তরা। তারা ছিল প্রায় দু-শো ঘর। মাছের চালানি কারবার করত তারা। স্টিমারঘাটে বরফ দিয়ে কলকাতায় এত মাছ তারা পাঠাত যে স্টিমারকে কোনো কোনো দিন তারা দু-ঘণ্টাও আটকে রাখত। এখন তারা আর বেশি কেউ নেই, দু-এক ঘর হয়তো আছে। জেলেরা রাস্তার পারে মেলে দিত কতরকমের জাল-ইলিশধরা, চিংড়িমারা, নদীবেড় দেওয়া। তারা সব দেশ ছেড়ে এসে নবদ্বীপের আশপাশে ‘হা গৌরাঙ্গ’, ‘হা গৌরাঙ্গ’ করছে এখন। কুমোরদের সংখ্যা খুব ছিল না বটে, তবে দুটো বাড়িতে হাঁড়ি-কলসি যা হত তাতে গ্রামের তৈজসপত্রের অভাব মিটে তো যেতই, তারপর তারা নৌকো করে বাড়তি হাঁড়ি-কলসি সুন্দরবনে বিকিয়ে দিয়ে নৌকোভরতি ধান নিয়ে ফিরে আসত ফি-বছর। তারা পাট উঠিয়ে কোথায় গেছে জানি না। এ ছাড়া ছুতোরপাড়া, কামারপাড়া নিয়ে এমন স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম আর কোথাও গিয়ে পাব কি না সন্দেহ। অভাব হয়তো ছিল, তবে অভাবের বোধ ছিল না বলেই জিনিসের অপ্রতুলতার কথা শোনা যায়নি সে গাঁয়ে।
বারোমাসে তেরো পার্বণ, আর তার ঘটাও ছিল তেমনি। দেখতে দেখতে কার্তিক মাস পড়ে যেত। ধান ঘরে উঠেছে, পথঘাট কিছু শুকিয়েছে, লেগে গেল বরোয়ারি কালীপুজোর ঘটা এ উপলক্ষে। ভদ্র পাড়ায় হত কালীর আসরে যাত্রাগান, শখের থিয়েটার, কবিগান, জারিগান। হিন্দু-মুসলমান চাঁদা দিয়ে, পান তামাক খেয়ে একত্রে গলাগলি করে রাতের পর রাত গান শুনত–কবিদের গানের লড়াই, ছড়ার কসরত শুনে তারিফ করত। মদন কবিওয়ালা, ছমির বয়াতি উভয়েরই ছিল গ্রামের মহলে মহলে সম্রাটের সম্মান। চৈত্রসংক্রান্তি, রথ ও দোলের মেলায় গ্রামে চলত সস্তা বিপণির বিকিকিনি, কত ভিন গাঁয়ের কত জিনিসের হত আমদানি! চার পয়সা, আট পয়সার পুতুল থেকে এক পয়সার বাঁশি পর্যন্ত কিনে আমরা কত যে সুখী হয়েছি, সে সুখ আর কি ফিরে পাব? দশহরাতে নিজেদের দুর্গাপ্রতিমা নিয়ে জেলেদের বড়ো বড়ো ছাদি-নৌকোয় বের হতুম আমরা। সাতখানি প্রতিমার সঙ্গে চৌদ্দজন ঢাকি বিসর্জনের বাজনা বাজিয়ে মরাগাঙের স্থির জলে বেদনার মূৰ্ছনা বইয়ে দিত। দু-পারের হিন্দু-মুসলমান গৃহবধূরা সজল চোখে বিদায় দিত দেবী জগন্মাতাকে। বাইরের নৌকোতে ঘুরে ঘুরে খঞ্জনিতে তাল ঠুকে গাইত মুসলমান বয়াতি বিদায়ের বিসর্জন গান। দশহরার পরের দিন সকল বাড়িতেই লেগে যেত তাড়াহুড়ো। মাইলখানেক দূরে বাহাদুরপুরের ঘাটে যেতে হবে ইছামতী নদীর কিনারায়। ওইখানেই হত নৌকোবাইচ–এক-শো হাতের, আশি হাতের লম্বা নৌকোয় পাল্লা দিয়ে বেয়ে আসত কত শত শত নৌকো নীল, লাল, সবুজ নিশান উড়িয়ে। সব নৌকোই মুসলমান মাঝিদের–গলুইয়ের ওপর কালো বাবরি উড়িয়ে, পিতলে বাঁধানো বৈঠা ঘুরিয়ে পঞ্চাশ-ষাট জন বাইচ-খেলোয়াড়কে সমান তালে, সমান জোরে জল টেনে চলতে তারা সংকেত করত। এ যেন মহাযুদ্ধের প্রধান সেনাপতির ইঙ্গিতে যুদ্ধ করে চলেছে সৈন্যদল–সেনাপতি অলক্ষ্যে নন, পুরোভাগে। প্রতিযোগিতা চলত দেশবিদেশের নৌকোয়, পাল্লা দিত গ্রামে গ্রামে, মহকুমা মানিকগঞ্জের পরগনায় পরগনায়। যে বছরে পাটের দাম যত বেশি মিলত, সেই বছরে তত জোর পাল্লা। হারজিতের সমাধান কোনোদিন দেখতে পেতুম না, কারণ কোথায় যে ওই পাল্লা শেষ হত, কত মাইল দূরে, তা শুধু ইচ্ছামতী নদীই বলতে পারত। আমরা দেখতুম শুধু উল্কাবেগে ছুটে চলেছে এক এক জোড়া নৌকা। নয় তো দেখেছি, ধীরে ধীরে বেয়ে চলেছে একখানি বাইচের নৌকো–চার-পাঁচজন বয়াতি গায়ক ঘুঙুর পরে নেচে নেচে খঞ্জনি বাজিয়ে গেয়ে চলেছে বয়াতি গান–নিজেদের রচনা, বর্তমান যুগধারা ও অতীতের সুখ-দুঃখের ব্যঙ্গ প্রকাশ। দেশ ভাগ হবার পরে শেষ গান শুনেছি বয়াতির কণ্ঠে বিষাদের সুরে,
কলি যুগে জান বুঝি আর বাঁচে না–
কোথায় থেকে তুফান আইল,
ঘর বাড়ি সব উড়াইয়্যা নিল,
মানুষজনে খাইত্যাছে আইজ কুত্তা শিয়ালে।
সেই বয়াতি সুরের বিদায়ক্রন্দন আজও কানে বাজে–কলকাতার সুর-লয় সংযোগে আভিজাত্যমন্ডিত যেসব ভাটিয়ালি গান আজ শুনছি, তার চাইতেও গভীর করে যে সেই বৈঠার তাল, খঞ্জনির মূৰ্ছনা মনেপ্রাণে দাগ কেটে রেখেছে। তেমনটি কি আর শুনব? ছন্দহীন পঙক্তিবিহীন সেই গেঁয়ো কবির মর্মভরা কবিতা, ইচ্ছামতীর জলেই কী চিরকালের মতো বিসর্জন দিয়ে এলাম?
পৌষ মাস এসে পড়ল। এর সময়েই হত আলিজান ফকিরানির দরগায় বছরের উৎসব। সারামুলুকের হিন্দু-মুসলমান ছুটে যেত ফকিরানীর আশীর্বাদ, দোয়া নেবার জন্যে। তার দরগা দুধে দুধে ধুয়ে দিত, তার সর্বজনীন সিন্নির খিচুড়ি মাথায় করে নিয়ে যেত হিন্দু-মুসলমান সবাই। পঙ্গু ফকিরানী তাঁর রুক্ষ জটাজালপূর্ণ মাথাটি নাচিয়ে নাচিয়ে একবার এর আর ওর গলা জড়িয়ে ধরে ‘আল্লার জান, বাঁচো’ বলে ছুটতেন এধার-ওধার। হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদ ভুলে এই গেঁয়ো তাপসী রাবেয়া’র আশীর্বাণী মাথায় করে কৃতার্থ হত সবাই। মকিম শেখের কোলে চড়ে কতবার গেছি সেই প্রসাদী সিন্নি খেতে। সেই ফকিরানীও আজ নেই–সিন্নিও ফুরিয়ে গেছে। দরগা নাকি পদ্মার জলে অতলে তলিয়ে গেছে। ভোর হলেই এখনও কানদুটো শুনছে শেষরাতের আজানধ্বনি, উদ্ধব বৈরাগীর উদাসিয়া গান। চৈত্র মাসের কালীকাঁচ আর বুড়ো মোল্লার বহুরূপ এখনও যে চোখের সমুখে নেচে বেড়ায়! ঘোষালের যাত্রার আসরে ভীমের গদা এখনও যে বনবন করে মনের চোখের সামনে ঘুরছে!
কলকাতায় পথে-ঘাটে কতরকমের পাগলই না দেখছি–তবু দিনু পাগলাকে ভুলতে পারি না। সেই দিনু শেখের মেয়েটাও মরে গেল–আগের বছর বউ মরেছে কলেরায়, দিনু পাগল হয়ে গেল। ঘন কালো সুঠাম দেহে, একমাথা ঝাঁকড়া কালো চুলে সে পরত বেছে বেছে ধুতরো ফুল। সুদে ও তস্য সুদে তার ভিটেমাটি আগেই গ্রাস করেছিল মহাজনরা–তাই ছিল না তার কিছুই। কালীতলায় পড়ে থাকত রাতের বেলায়, দিনভর বসে থাকত সে পদ্মার ঘাটে। বউ-ঝিরা তার রক্তচক্ষু দেখে একটুও ভীত হত না–আর দিনুর কড়া পাহারায় একটি বাচ্চাও জলে ডুবতে পারত না। একটু বেকায়দায় পড়ে গিয়েছে তো–দিনু ডাঙা থেকে লাফিয়ে পড়েছে–জল থেকে তুলেছে ডুবন্তকে। খিদের বেলায় একটা কলাপাতা নিয়ে যেমন খুশি ঢুকে পড়েছে যেকোনো বাড়িতে–পেয়েছে পেটভরা ভাত। স্ফুর্তি করে খেয়ে ‘আল্লাকালী’, ‘আল্লাকালী’ বলে লাফাতে লাফাতে ছুটে চলে গেছে বাইরে, দু-চোখের বাইরে। কিছুক্ষণ বাদেই দেখা যেত তাকে, চাষির হাতের লাঙল কেড়ে নিয়ে সে চালাচ্ছে বলদ—’হেঁইও–হট’–ততক্ষণে আইলের ওপর বসে চাষি ভাই একটু তামাক খেয়ে নিচ্ছে। সে আর কতক্ষণ! একটু পরেই দিনু ছুটেছে পদ্মার তীরে।
সেই শান্ত পাগল দিনুই একবার ভীষণ কান্ড করে বসল। শীতের মধ্য রাত্রি, হরি পোদ্দারের খড়ের গাদায় আগুন লাগিয়ে দিয়ে সে জোর চেঁচাতে শুরু করল-”ও পোদ্দার মোশাই–দ্যাহেন কত্তা, কী নাল ঘোড়া দাবাড় দিছি। যত লোকজন হই-হুঁল্লোড় করে আগুন নেভায়, দিনু ততই নাচে বগল বাজিয়ে, কী সুকর্মই না সে করেছে। অগ্নি নির্বাপিত হল। তারপরে গাঁয়ের মাতব্বর ব্যক্তিরা বসে গেলেন বিচার করতে। পঞ্চায়েতি বিচার করতে। পঞ্চায়েতি বিচারসভায় হিন্দু-মুসলমান দাস-কৈবর্ত সকলেই থাকতেন। দিনুকে জিজ্ঞাসা করা হল, কেন সে এমন কাজ করল। সাফ উত্তর দেয় দিনুজারা, বড়ো কড়া জারা (শীত)। সেই বছর থেকে যেবারই বেশি শীত পড়েছে, গাঁয়ের লোকে চাঁদা করে দিনুর জন্যে শীতের কম্বল কিনে দিয়েছে, নয় তো জোগাড় করে দিয়েছে। দিনু আর শীতেও কাঁপেনি–লাল ঘোড়াও আর ছুটোয়নি। দিনু আর নেই। কিন্তু কলকাতায় এসে দেখি সেই দিনু পাগলার মৃত্যু হয়নি। সারাদুনিয়ার ঘরে ঘরে দিনু পাগলার জন্ম হয়েছে–তারা ছুটিয়ে আসছে লাল ঘোড়া। এবার হরি পোদ্দারের দলের যে কী দশা হবে ভেবে পাইনে কিছু, তাদের রুখতে হলে যে কম্বলের দরকার, তা দেবে কে?
চৈত্র মাসের খরার দিনে দেখতুম গাঁয়ের চাষি-ছেলেরা মাঙনে বের হত। ঝকঝকে একটা ঘটি হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে, গোরুর দড়ি দিয়ে আম্রপল্লব-বাঁধা পাঁচন বাড়ি কাঁধে নিয়ে ঘরে ঘরে সিন্নির চাল মেগে নিত। বলত একদিলের সিন্নির চাল দেন। কোন আল্লাদেবতা যে এই ‘একদিল’ জানতুম না। এখন বুঝি একদিল মানে একপ্রাণ। এত বড়ো দেবতার কৃপা কুড়োতে হিন্দু ও মুসলমান চাষিদের মধ্যে বিভেদ হত না। সেই ভিক্ষালব্ধ চাল দিয়ে সম্মিলিত যে সিন্নি পতিত ভিটেয় হত–তাতে হিন্দু-মুসলমান সবাই যোগ দিয়ে বৃষ্টির কামনা করত। মন্ত্রতন্ত্র কিছু ছিল না। একপ্রাণের কামনার ফল ফলত বই কী–হয় শীঘ্র, নয় বিলম্বে।
সেই ছেড়ে-আসা অবিখ্যাত আমার গ্রাম! কলকাতার মিলের চিমনি ভোরের বেলাতে ভোঁ করে ওঠে-ঘুম ভাঙতেই শুনি! মনটা রোজই ছ্যাঁৎ করে ওঠে। ওই গোয়ালন্দের স্টিমার কাঞ্চনপুরঘাট ছেড়ে এসেছে–যাবে নারায়ণগঞ্জে, বাঁশি বাজাচ্ছে–ভোঁ-ভোঁ।
.
সোনারং
খাওয়া পরা দেখছি হল ভার,
মায়ের মুখ কেবল মনে পড়ে;
তাদের কথা বলছ কিবা আর,
দূর থেকেও সঙ্গ নাহি ছাড়ে।
খাওয়াপরা সকল দিছি ছেড়ে,
ছেলেগুলোই সব নিল রে কেড়ে!
কতকাল আগে কোন কবি এ গান গেয়ে গেছেন তা সঠিক না জানলেও তাঁর দুঃখের সঙ্গে আমাদের দুঃখের মিল দেখে আশ্চর্য বোধ করছি। আজ আমরা জন্মভূমি ছাড়া হয়ে নাওয়া খাওয়া ত্যাগ করেছি, আমরা মাকে ভুলতে চাইলেও তিনি চোখের সামনে উঠছেন ভেসে বার বার। স্মৃতিসঙ্গ কিছুতেই মুক্তি দিচ্ছে না,–তাঁর দুরন্ত ছেলেগুলো তাঁকে কেড়ে নিয়েছে আমাদের কাছ থেকে! মাকে ছেড়ে প্রবাসী হয়েছি, প্রবাসযাত্রার শেষ কবে হবে জানি না।
বার বার মনে পড়ছে আমার গ্রাম সোনারং-এর কথা। আশা-নিরাশার স্মৃতি মনের মণিকোঠায় ভিড় করে রয়েছে জট বেঁধে, মন হাঁপিয়ে উঠছে চারপাশের দেওয়াল-ঘেরা শহুরে আবহাওয়ায়। এখানে মুক্তি নেই, উদারতা নেই, ছুটি নেই, ফাঁক নেই। আমার গাঁয়ের উন্মুক্ত প্রান্তরের উদার হাতছানি কোথায় পাব শান-বাঁধানো কলকাতার বুকে? হৃদয়বীণার তারে মরচে ধরেছে–তাকে হয়তো আর সুরে বাঁধতে পারব না! সুর কেটে যাচ্ছে তাই বার বার।
আমার গ্রামটির ইতিহাস শান্তির ইতিহাস। ঐতিহাসিক ঐতিহ্যে সে গ্রাম মহান। আজও সেখানে বৌদ্ধযুগের শান্তির ধ্বজা উড়তে দেখা যায়। সেখানে রয়েছে বৌদ্ধযুগের ধ্বংসাবশেষ। গ্রামের কবি হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত মশায়ের কাছে শুনেছি সেই আলো-ঝলমল তথাগতের শান্তির ললিত বাণীর মনোরম গল্প। আজও বর্ষার দিনে যেখানে বাঁকাজল খেলা করে তার তলায় বিশ্রাম করে তথাগতের সারিবদ্ধ সোনার দেউল। জন্মভূমি পক্ষবিস্তার করে রক্ষা করছেন বিস্মৃত ইতিহাসকে। ভারতবর্ষের এই শ্রেষ্ঠ সন্তানের জন্যেই চিন-জাপান পর্যন্ত ভারতকে গুরু বলে স্বীকার করে নিয়েছে। তাঁর শান্তির বাণীকে বর্বর মানুষ আর ব্যর্থ পরিহাস করতে পারবে না–সলিলসমাধি সৌধরেখা আজ জলরেখায় গেছে মিশে! মনে পড়ে প্রথম যেবার ঢাকা শহরে ক্ষুদ্র মিউজিয়ামটি দেখতে যাই, সেবার প্রথমেই দেখতে পাই সুউচ্চ স্কুপের ওপর ভগবান বুদ্ধের স্তব্ধ মূর্তিটি। আপনা আপনিই সেদিন তাঁর পায়ে আমার মাথা পড়েছিল লুটিয়ে। সেখানে দাঁড়াতেই কানে বেজে উঠেছিল কবিরাজ গোস্বামীর গানটি,
উপজিল প্রেমবন্যা, চৌদিকে বাঢ়য়।
জীবজন্তু কীট আদি সকলে ডুবায়।
বুদ্ধের অনন্ত মাধুরীপূর্ণ প্রেম ও দয়ার অমৃত মন্ত্র পুণ্যবতী বাংলা মাকে তো বাঁচাতে পারল না? বর্ষার স্ফীতবক্ষা পূতসলিলা জাহ্নবীধারার মতো হিংসা-দ্বেষকে তো প্রেমবন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারল না মানুষ! হৃদয়-আত্মা বাসনাহীন নির্লোভ হয়ে চিদাকাশে বেলুনের মতো অদৃশ্য হতে পারে না কি? কেন আজ আমাদের পদে পদে পরাজয়ের গ্লানি। সংসারী মানুষ ইন্দ্রিয়সুখের জন্যে আর কত নীচে নামবে? শাক্যসিংহের মতো আজ আমাদের কে বলবেন, ‘সকলই জ্বালাময়। কীসের অগ্নিতে জ্বলিতেছ? আমি তোমাদিগকে বলিতেছি,-ক্রোধের জ্বালায় দগ্ধ হইতেছ,–মোহের শিখায় দগ্ধ হইতেছ!’
সেদিন বুদ্ধমূর্তির সামনে একটি ফলক দেখে চমকে উঠেছিলাম,–মূর্তিটি আমার গ্রামের একটি পুষ্করিণী খননকালে পাওয়া গেছে। জানি না সেই সদাহাস্যময় বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্তি আজও ঢাকার জাদুঘরে শোভা পাচ্ছে কি না! যাঁর চরণতলে একদিন কোটি কোটি মানুষ নিয়েছিল শান্তির পাঠ, আজ তিনিই শান্তিতে আছেন কি না ভাবতে হচ্ছে। সর্বদেশে সর্বকালেই দেশের বুকে জগাই মাধাই মাথা নাড়া দিয়েছে, কিন্তু এরা কি শেষ পর্যন্ত ভুল বুঝতে পারবে? পারবে তো আবার সবাইকে বুকে টেনে নিতে? আমাদের আশা ব্যর্থ হবে কি না জানি না, কিন্তু সেই সুদিনের প্রতীক্ষাই করছি সব সময়।
স্টিমারঘাটে নামতে নামতেই শরীরে জাগত কেমন অনির্বচনীয় একটা রোমাঞ্চ, সোনালি স্বপ্নের আবেশে মন হয়ে উঠত আবেশময়, সেখান থেকেই পেতাম সোনারং-এর পরশ। মাঝিদের আহ্বানে চমক ভাঙত হঠাৎ। কানে এসে বাজত–’আহেন কর্তা, আমার নায়ে আহেন, যাইবেন কৈ?’ দরদস্তুর বা কথাবার্তার মধ্যে না গিয়ে শুভ্র-শ্মশ্রু বৃদ্ধ মাঝির নৌকোয় গিয়ে উঠে পড়তাম বাক্স-বিছানা নিয়ে। আমার নির্লিপ্ত ভাব দেখে মাঝি কী বুঝত জানি না, তবে আশ্বাস দিয়ে বলত, “আমিই যামু কর্তা, ভারা যা অয় দিয়েন অনে!’ নৌকোয় আরাম করে হাত-পা ছড়িয়ে বসার পর প্রশ্ন করতাম, “সোনারং চিনো?’ হাসতে হাসতে সে জবাব দিত, ‘হোনারং চিনি না? কন কী কর্তা, হেই দিনও আইলাম আপনেগ গেরাম থিঙ্কে। সুতরাং আর চিন্তা কী? পাটাতনে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ি নিশ্চিন্ত আরামে! নৌকো ছাড়া অন্য যান কিছু নেই গ্রামে যাওয়ার। গ্রাম পত্তন যিনি করেছিলেন তিনিও এসেছিলেন এই নৌকো করেই মনের খুশিতে গান গাইতে গাইতে। বেতবন আর হিজলের বুক চিরে নৌকো ঠিকই পথ চিনে বার বার এসেছে গেছে যাত্রী বুকে নিয়ে। আজ ভাবি সে জঙ্গলে যে শয়তান লুকিয়ে ছিল তা কারও নজরেই পড়েনি।
নৌকো ভ্রমণ চুপচাপে হয় না,–পেঁচার মতো মুখ করে আর যাই করা যাক নৌকোতে বেড়ানো যায় না। তাই মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে মাঝির সঙ্গে আলাপে রত হতাম। আলাপ জমাতে মাঝিদের কেউ বলে চাচা, কেউ বলে মামু। আমি মামু বলেই গল্প আরম্ভ করতাম। পেটে তখন পদ্মার বাতাস ক্ষুধার উদ্রেক করেছে, তাই আমার প্রথম কথা ছিল সেদিন, ‘মামু, খুদা তো বড়ো লাগছে, বাজার-টাজার আছে নাকি সামনে?’ আন্তরিকতায় মাঝির মুখও দেখেছি সেদিন ব্যথাতুর হয়ে উঠেছে। আমার খিদে তার বুকেও এনেছে ব্যথার পরশ-ম্লান হয়ে সে জবাব দিয়েছে, আগে কইলেন না ক্যান, এই তো দিগির পারের আটটা ছারাইয়া আইলাম। আইচ্ছা, সামনে পুরার বাজার আছে, চিড়া-মুড়ি কিন্না দিমু অনে!’ কী সহানুভূতি, কত দরদ পেয়েছি সেদিন। মাঝিকে নিজের পরিবারের লোক বলেই মনে হয়েছে। কিন্তু আজ? কোথায় গেল সে সরল সহজ মামু! প্রাণভরা, দরদভরা সহানুভূতি দিয়ে যারা মানুষকে বুঝত তারা কি চিরবিদায় হয়েছে এই কলুষ-পঙ্কিল পৃথিবী থেকে? না চক্রান্তকারীদের ভয়ে মুখ তারা খুলতে দ্বিধাবোধ করছে? সৌন্দর্যের মৃত্যু হওয়া দেশের পক্ষে চরম লোকসানের কথা–সেই অশুভ দিন কেন নেমে এল কালো পাখা মেলে এই বাংলার ওপর?
সেদিন মাঝির সঙ্গে ভাগ করে চিড়ে-মুড়ির পর খালের জল খেয়ে যে কত আনন্দ পেয়েছি তা ভাষায় বলা যায় না। পদ্মার বাতাস, পদ্মার জল সেদিন কাছে টেনে নিয়ে ভাই-ভাইয়ের একপ্রাণতা একতার সূত্রে বেঁধে দিয়েছিল,–আজও সেই পদ্মা আছে, কিন্তু সে তো আজ চুপচাপ সাক্ষীর মতো ভ্রাতৃবিরোধ দেখে যাচ্ছে। ইচ্ছে করলে পারে কি সে আমাদের সকলের হাত এক করে দিতে! পদ্মার জলের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের চোখের জল। কীর্তিনাশা বলে তার বদনাম আছে, কিন্তু তার কীর্তিকথার খোঁজ আমরা ক-জন রাখি? মানুষ কি তার চেয়েও বেশি কীর্তিনাশ করেনি? মানবতাবাদের সংহার কে করেছে? মানুষ, না পদ্মা? আজ ঘুমের মধ্যে পদ্মার ঢেউ বুকের ভিতর আছাড় খেয়ে পড়ে সমস্ত অভিমান নিয়ে। সে ঢেউ কি আর কারও বুকে লাগে না?
এক-একটি ভাব মানুষের মনে এক একরকম প্রেরণা জোগায়। তা না হলে যে পদ্মা রবীন্দ্রনাথের মনে কাব্যের প্লাবন এনেছিল সে পদ্মাই কী করে মারণমন্ত্রের প্রেরণা দিল? কবিতার প্রেরণা ও লুণ্ঠনের প্রেরণা কী একই উৎসকেন্দ্র থেকেই উঠছে না? পরস্পরবিরোধী এ ভাব কেন জাগে হৃদয়তন্ত্রীতে? সুকুমার বৃত্তির চিরউচ্ছেদ হতে পারে না মানুষের মন থেকে। এই সাময়িক ক্ষিপ্ততার শেষ হবেই হবে।
শহুরে সন্ধ্যায় চিমনির ধোঁয়া দেখলে আমার সেই মাঝির তামাক খাওয়ার কথা মনে পড়ে। হুঁকো কল্কে সাজিয়ে ধূম্রকুন্ডলীর যে আবর্ত সেদিন তারা সৃষ্টি করেছিল তা থেকেই বোধ হয় আরব্য উপন্যাসের দৈত্যটা প্রবেশ করেছে তাদের মনে! এ দৈত্যের সংহারমন্ত্র কী? তাকে আবার কি বোতলে ঢোকাতে পারা যাবে না?
দু-হাতে বৈঠা মারতে মারতে নৌকো যেত এগিয়ে। ছোটো খালের দু-ধারে কত রকমের গাছ। যোগীর জটাজালের মতো মাটির ওপর দিয়ে শিকড়গুলো এসে নেমেছে খালের জল ঘেঁষে। সেই বিরাট গাছের ধ্যানরত স্তব্ধতা, অনন্ত নীলিমার দিকে চেয়ে থাকার ছবি আজ ভুলতে পারছি না। তাদের ধ্যান বোধহয় আজও ভাঙেনি,তারা শান্তিতে থাকুক, মনে গৈরিক ধূসর বৈষ্ণবতা এনে মানুষকে আবার সুখীসচ্ছল করুক এই প্রার্থনাই করি দূরে বসে।
মাঝে মাঝে বেতের ঝোঁপ। বিক্রমপুর আছে অথচ বেতবন নেই এটা কল্পনাই করা যায় না! ঘন জঙ্গল সৃষ্টি করে কত রকমারি পশু-পাখিকে আশ্রয় দিয়েছে এই বেত। এই খালের ধারের বেত ঝোঁপের বুক থেকেই ভোরের কাকলি ওঠে প্রথম। নির্জন দুপুরে ঘুঘুর ডাক ওঠে এখান থেকেই, এখান থেকেই নিশুতি রাত্রে ককিয়ে ওঠে বক-শিশুরা! জঙ্গলের সঙ্গে যোগ দিয়েছে কচুরিপানার বংশ। বিক্রমপুরের শ্বাসরোধ করার চক্রান্ত এরা কোথা থেকে পেল? বিক্রমপুরের সঙ্গে সমস্ত পুববাংলার লোকের শ্বাসরোধ কি এই রক্তবীজের বংশধরেরাই করেছে?
খালের ঘাটে গৃহস্থ বধূরা জল নেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে কটাক্ষে দেখে নিত হাট-ফিরতি নৌকোর আরোহীদের। তাদের মুখে খুঁজে পেতাম যেন রাঙা বৌদি, মণিদি, মনোপিসির মুখের আদল! প্রবাসী মন থেকে উৎপাটিত হয়ে তারা নানান দিকে পড়েছে ছড়িয়ে, জানি না তারা আজকে কোথায়। জানি না তাদের ক-জনই বা নির্বিঘ্নে চলে আসতে পেরেছে সম্মান বজায় রেখে। দিকে দিকে মেয়েদের অসম্মান–তাদের আতাঁরবে মা বসুন্ধরার কি ঘুম ভাঙবে? নারীর লজ্জা কি নারী চোখ মেলে দেখেই যাবে শুধু? দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে, সংকুচিত হয়ে আর কতদিন ভারতবর্ষ থাকবে? নারীর সম্মানের জন্যে আগে মানুষ কেমন উত্তেজিত হত, নারীরা আসন পেত সবার ঊর্ধ্বে। নারীর অসম্মান তখন সমগ্র দেশের অসম্মান বলে বিবেচিত হত, সেদিনের সে মনোভাব গেল কোথায়? হিন্দু-মুসলমান, শিখ, খ্রিস্টান চিরদিনই নারীকে সম্মান দেখিয়েছে, অথচ আজ এ কী হল? জাতি-বিচারই কি নারী-বিচারের মাপকাঠি হয়ে মনুষ্যত্ববোধের অধঃপতন ঘটাবে বাংলায়?
রাজ্যের ভাবনা ভাবতে ভাবতে কখন যেন একটু তন্দ্রা এসে যেত। সে তন্দ্রা টুটত বৃদ্ধ মাঝির সস্নেহ ডাকে, ‘উঠেন কর্তা, টংগীবাড়ি আইয়া পড়ছি। টংগীবাড়ি এসে পড়েছি? তাহলে তো এসেই পড়েছি। মনে পড়ে যায় কতদিন এখানে এসেছি হাট করতে; হাট সেরে অকারণ দাঁড়িয়ে থাকতাম ওই পুলের ওপর। গ্রাম-সম্পর্কে মতিকাকার মাল কাঁধে বয়ে পৌঁছে দিয়েছি তাঁর বাড়িতে কতদিন। বাড়ি হাজির হয়ে মতিকাকা বাতাসা দিয়ে জল দিতেন আদর করে। তারপর হেসে বলতেন : “আরে আদা শুকাইলেও ঝাল থাকেরে, তগ মতন বয়সে আমরা দুই মুনি আড়াই মুনি বোঝা লইয়া আইছি টংগীবাড়ির থন। সেদিনের গল্পগুজবের মধ্যে মতিকাকা, মতিকাকিমার সহৃদয়তা আমাদের মুগ্ধ করত। মুড়ি, বাতাসা, নারকেল নাড় আমাদের বারবার টেনে নিয়ে যেত মতিকাকার বাড়ি! জানি না, ঝড় তাঁদের কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গেছে আজ। যেখানেই হোক, সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন! বেঁচে থাকলে দেখা হবেই একদিন-না-একদিন। দুঃখ লাগে ভেবে, যারা মুড়ি নাড় বিলি করেছে বেহিসেবিভাবে আজ তারাই করুণ চোখে তাকিয়ে থাকে খাবার জিনিসের দিকে! কপালের পরিহাস আর কাকে বলে জানি না, কিন্তু নিজেদের দৃষ্টান্ত থেকে তার পরিচয় পাচ্ছি। সামান্য ডালভাতের জন্যে আজ আমাদের স্বার্থপরতা দেখে স্তম্ভিত হচ্ছি।
টংগীবাড়ির পর মনে পড়ছে মুনশিবাড়ির কথা। নবাবি আমলে এই গ্রাম আটকে গিয়েছিল বিলাসের ফাঁসে। চরম মুনশিয়ানা করে গেছে গ্রামবাসীরা। চিহ্নস্বরূপ আজও মঠ-মসজিদ দেখা যায় প্রচুর। মঠে শ্মশানেশ্বর শিব ও মা কালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে সেই নবাবি আমল থেকে। মা কালী ছিলেন এ অঞ্চলের জাগ্রত দেবতা। কত দূর দূর গ্রাম থেকে লোক আসত পুজো দিতে ধন্না দিয়ে অভীষ্টসিদ্ধির জন্যে! দেখেছি মুসলমান ভাইয়েরাও হাতজোড় করে মানত করে যেত। কিছুদিন বাদে রোগমুক্তির পর জোড়া জোড়া পাঁঠা নিয়ে আসত দিকে দিকে আনন্দধ্বনি ছড়াতে ছড়াতে। জাতিধর্মনির্বিশেষে এমনি কালীপূজো আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না, কিন্তু মা কালীও কেন বিরূপ হলেন আমাদের ওপর? কেন ভিটে ছেড়ে নির্বাসিত হলাম, অজানা ভবিষ্যতের অন্ধকারে ঝাঁপ দিতে হল কোন পাপে! ছোটোবেলায় এই মঠবাড়িই ছিল আমাদের আড্ডাখানা। কত দৌরাত্মই না করেছি আম-কাঁঠালের সময়। গভীর রাত্রে খেজুরের রস চুরি করে জলভরতি কলসিটি টাঙিয়ে রাখতাম ভালো মানুষের মতো।
বিজয়া দশমীর দিন কী মাতামাতিই না করতাম এই মঠের ঘাটে। ঢাক-ঢোলের বোলের সঙ্গে চার ধূপতির আরতি দেখে মাঝরাত্রি পর্যন্ত হইহুল্লোড় করে কাটাতাম। দুর্গাপুজো উপলক্ষ করে কোনো বছর ছুটিতে বাড়ি যেতে না পারলে অস্থির হয়ে পড়তাম আগে। এখনও বছরে বছরে যথারীতি পুজো আসে, কিন্তু আমি বাড়ি যেতে পাই না। এ দুঃখের তুলনা দেব কীসের সঙ্গে? অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠছে চোখ দুটি পূর্ব সুখস্মৃতির কথা ভেবে। আজও সে মঠ আছে, তাকে নিশানা করে লোকেরা হয়তো চলাফেরাও করে ভক্তিনম্রভাবে মা কালীকে প্রণামও হয়তো করে কেউ কেউ, কিন্তু সেদিনের সেই সুখী উজ্জ্বল আবহাওয়া কি আর আছে মুনশিবাড়িতে? একতা, সংঘবদ্ধতাকে নির্বাসন দিয়ে মানুষ আজ যে ভুল করল তার উপলব্ধি কবে হবে কে জানে!
মঠের কথা কিছুতেই ভুলতে পারছি না আজ। বহু স্মরণিকা ভিড় করে আসছে–এই মঠই ছিল এ অঞ্চলে অগ্নিযুগের প্রেরণাকেন্দ্র। অনুশীলন পার্টির অন্যতম প্রধান কার্যালয়। পুলিশের অত্যাচার এ কেন্দ্রে ঘূর্ণিবায়ুর মতো নিষ্ঠুর গতিতে বয়ে গেছে এক সময়। সে বর্বরতার কথা মনে করলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। গ্রামের দেশকর্মী ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে কতরকম মর্মান্তিক অত্যাচারই না করেছে অমানুষ অশিক্ষিত মূঢ় সেদিনকার ইংরেজ ভৃত্যরা। তাদের ভয়ে তরুণ যুবকদের গ্রামে থাকাই হয়ে উঠেছিল অসম্ভব। সেই সময় থেকেই নীরব ফন্তুর মতো কাজ হত মঠে–মা কালী তার সাক্ষী। সেদিন বিদেশি শক্তির বিপক্ষে মায়ের খঙ্গ উঠেছিল ঝলসে, মায়ের আশীর্বাণী পেয়েছে সব ভক্ত ছেলের দল। কিন্তু ভ্রাতৃবিরোধের দিনে মা রইলেন নীরবে দাঁড়িয়ে, অথচ তাঁর আশীর্বাদের প্রয়োজন তখনি ছিল বেশি!
মনে পড়ছে এ গ্রামের কৃতী নারী-পুরুষের কথা। এখানকার কেউ হয়েছেন নামকরা অধ্যাপক, কেউ আই. সি. এস., কেউ স্বাধীন ভারতের প্রতিনিধি হয়ে ইয়োরোপ গেছেন। এই গাঁয়ের একটি মেয়ে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি পেয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছেন সর্বপ্রথম। তবুও বলব এঁরা গ্রামের মাটি থেকে বহুদিন থেকেই উৎপাটিত–প্রাণের যোগ তাঁদের নেই গ্রামের সঙ্গে। তাঁরা মহীরুহ, সামান্য ক্ষণের জন্যে বসা যায় তাঁদের ছায়ায়, কিন্তু আড্ডা জমাতে হলে যেতে হয় জেলেপাড়ার মহানন্দের বাড়ি, কিংবা প্রসন্ন মুদির দোকানে, না হয় বিশ্বম্ভর পালের হাঁড়ি গড়বার চাকের ধারে! তাদের সুখ-দুঃখই সারাগ্রামের সুখ-দুঃখ। তাদের প্রাণচাঞ্চল্য, তাদের আন্তরিকতা আজও নির্জন জীবনে রোমাঞ্চ জাগায়। মনে পড়ছে, সেবার অনাবৃষ্টি সম্বন্ধে আলাপ করতে করতে আমি বলেছিলাম যে, এবছর শীত যেমন দেরিতে এসেছে, বর্ষাও আসবে তেমনি দেরি করে। আমার কথা শুনে কালী ভুইমালী কারণস্বরূপ বলেছিল, ‘পাঁচ রবি মাসে পায়, ঝরায় কিংবা খরায় যায় সেদিন সত্যিই লজ্জা পেয়েছিলাম এই ভেবে যে, কতকাল আগের গাণিতিক গবেষণার ওপর প্রতিষ্ঠিত খনার বচনকে যারা প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় অনুসরণ করছে তাদের ওপর পান্ডিত্য ফলাতে গিয়েছিলাম আমি। বাংলার লোকসংস্কৃতি তো এদের ভেতরেই ক্ষীণ হয়ে বেঁচে আছে আজ পর্যন্ত।
যে গ্রামে প্রতিমাসেই উৎসব থাকত লেগে, সেখানে আজ মানুষ খুঁজে বের করতে হয় শুনলাম। বাড়িঘর হয়তো দাঁড়িয়ে রয়েছে, ঘন জঙ্গল গজিয়েছে উঠোনে, আগাছা জন্মেছে দেওয়ালে দেওয়ালে। সেই তেঁতুলগাছটাও কি আছে? ঝাঁকড়া ওই গাছের নীচে বসত আমাদের আড্ডা। মনে পড়লে হুহু করে প্রাণ, আপনাআপনিই চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে তপ্ত অশ্রু। নির্বিঘ্ন জীবন কি আর আমরা ফিরে পাব না, সেইদিনের মতো কি আর আমরা বরুণ পুজোতে মেতে উঠতে পারব না ছেলে-বুড়ো মিলে? চৈত্র মাসে জলের জন্যে প্রার্থনা জানাতাম বরুণদেবের কাছে। চৈত্রের খর রৌদ্রের অবসানের জন্যে জলকাদা মেখে গ্রাম প্রদক্ষিণ করতাম দল বেঁধে। মেঘের দেবতাকে খুশি করবার মন্ত্র আওড়াতাম,
দেওয়ার মাললা মেঘারানি।
খাড়া ধুইয়া ফালা পানি।।
মেঘের উপর পুন্নিমার চান।
ঝপঝপাইয়া বিসটি লাম।।
সেদিনের এই মন্ত্র ছিল যেন অব্যর্থ। পাগলা হাতির মাতন নিয়ে ছুটে আসত মেঘ-বৃষ্টি ঝড়। জীবন হত শান্তিময়, নির্বিঘ্ন। আজকের মানুষের তাপিত প্রাণ কি ঠাণ্ডা হতে পারে না এই মন্ত্রে? আমাদের জীবনে কী নেমে আসতে পারে না আবার সেই আকাঙ্ক্ষিত শান্তিবারি? শান্তিময়, সুখীসচ্ছল দিন কি চিরতরে ছেড়ে গেল আমাদের? আজ বর্ষা নামলে বেলেমাছ ধরার কোনো উৎসাহই পাই না আর, অথচ একদিন রাতদুপুরে ছুটেছি ছিপ হাতে মৎস্য শিকারে! পদ্মা প্রমত্তা নদীর বুকে ডিঙি ভাসিয়ে গেছি মঠবাড়ির বড়োখালে। খালে খালে জেগেছে জীবনের ছোঁয়াচ, মাঠে মাঠে বাধাহীন জলধারা যাচ্ছে ছুটে, সে-ছবি আজও আমায় উতলা করছে! শ্মশানে প্রাণবসন্ত দেখা দিক আবার, আবার ছুটিয়ে নিয়ে যাক আনন্দ নিজের গ্রামে, শান্তিবারি ঝরে পড়ুক প্রতিটি মানুষের মাথায়। ভয় থেকে অভয়ের মধ্যে নতুন করে জন্মলাভ করুক দেশবাসী। জড়তা থেকে নবীন জীবনে আমাদের প্রতিষ্ঠিত করুক ঈশ্বর! আর শুধু দিনযাপনের প্রাণধারণের গ্লানি সহ্য হয় না–নিশিদিন রুদ্ধঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের ধূমাঙ্কিত কালি জীবনের গায়ে কালি লেপন করছে, জীবন খন্ড খন্ড হচ্ছে দন্ডে পলে ভাগ হয়ে! রবীন্দ্রনাথের মতো আজ আমি শুধু প্রার্থনা করি,
শ্যেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন করে ঊর্ধ্বে লয়ে যাও
পঙ্ককুন্ড হতে,
মহান মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি করে দাও মোরে
ত্রিপুরা – বায়নগর চান্দিসকরা বালিয়া কালীকচ্ছ
কালের খেলনার মতো আমার সেই ছোট্ট গ্রামটির কথা আজ মনে পড়ে। মনে পড়ে কাঞ্চনফুল আর সোনালতায় মাটির পৃথিবীর সে অপরূপ হাসি– সোনালু গাছের ফলে (আঞ্চলিক ভাষায় বানরের লাঠি) ঘুঙুরের বোলের মতো মিঠে আওয়াজ আজও যেন স্পষ্ট শুনতে পাই। শ্রাবণের থমথমে আকাশের দিগন্তে মেঘের তম্বুরা যেন কোন খেয়ালি দেবতার বিদ্যুৎ-আঙুলের ছোঁয়ায় গুরু গুরু মন্ত্রে কাঁপছে–টিনের চালায় চালায় বৃষ্টির নূপুর বাজছে ঝমঝম করে; ধ্বনিবর্ণময় বর্ষার সে কী অপরূপ ঘনঘটা! আবছা আলো-আঁধারে চূর্ণবৃষ্টির ধূসর চাদর মুড়ি দিয়ে বিশ্বচরাচর যেন মনের কাছে আসত ঘন হয়ে। মনে পড়ে ক্ষান্তবর্ষণ শ্যামলী মৃত্তিকার বর্ণাঢ্য রূপশৃঙ্গার : কচি পাতার ফাঁকে-ফাঁকে সোনালি রোদের খিলখিল হাসি, বৃষ্টি-ধোয়া কনক চাঁপার উজ্জ্বল হরিৎ আভা। দুপুরের তীক্ষ্ণ রোদে উদার উন্মুক্ত আকাশ যেন গুণীর কণ্ঠের গভীর-গম্ভীর কোনো উদাত্ত রাগিণীর মতো দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত টানা। বৈরাগীর একতারার মতো মেঠো পথ চলে গিয়েছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তে ব্যাকুল বাউল-উতলা বাতাসে ফসলের গান; তৃণশীর্ষে সূর্যের গুঞ্জন।
আরতির ধূপছায়ার মধ্য দিয়ে দেখা ঝাপসা দেবী প্রতিমার মতো আজও চোখে ভাসছে আমার সেই ছোট্ট গ্রামটি–তার মধ্যে দেখেছি রূপকথার খুঁটেকুড়নি মায়ের নির্বাক বেদনার প্রতিমূর্তি। কালের একতারায় তাঁর অশ্রুর অশ্রুত রাগিণী যেন ডানা-ভাঙা পাখির মতো আজ কেঁদে কেঁদে ফিরছে।
গ্রামের নাম বায়নগর। ত্রিপুরা জেলার ছোট্ট একটি গ্রাম। শোনা যায়, আসলে এর নাম ছিল নাকি ‘রায়নগর’। এ গাঁয়ের জমিদার ছিলেন রায়েরা। রায়বংশের শেষপুরুষ অঘোর রায়ের প্রতাপ ছিল দোর্দন্ড। পাকা সবরি কলার মত গায়ের রং, উন্নত ঋজু নাসা আর ভোজালির মতো একজোড়া তীক্ষ্ণ গোঁফ ছিল রায়ের। অঘোর রায় যেমন ছিলেন বাঘের মতো ভয়ানক তেমন তাঁর রাগও ছিল প্রচন্ড। আকস্মিক উত্তেজনার বশে একদিন তিনি এমন একটি কান্ড করে বসেন যার ফলে তাঁকে শেষপর্যন্ত এ গ্রাম ছেড়ে যেতে হয়।
ঘটনাটি সম্পর্কে জনশ্রুতি এরকম। বাড়ির লাগোয়া একফালি জমিতে তিনি নানা দূরদেশ থেকে প্রচুর অর্থব্যয় করে নানারকম বাহারি ফুলের চারা এনে লাগিয়েছিলেন। ফুল আর ফুলকপির চাষে ছিল তাঁর সমান আগ্রহ, সমান অধ্যবসায়। একদিন ভিন গাঁয়ের এক জমিদারনন্দনের সদ্য ক্রীত টাট্ট ঘোড়াটি মালির সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে বাগানে ঢুকে পড়ে। খবর শুনেই তো অঘোর রায়ের ব্রহ্মরন্ধ্রে বারুদ জ্বলে উঠল–দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দুর্গাপুজোর সময় যে খঙ্গ দিয়ে মহিষ বলি দেওয়া হত তাই নিয়ে ঝড়ের মতো ছুটলেন তিনি বাগানের দিকে। পেছনে পেছন ছুটল তাঁর স্ত্রী, পাইক, বরকন্দাজ আর সব। খঙ্গের শানিত চোখ দুটি রক্তের তৃষ্ণায় ধকধক করে জ্বলছে, আর জ্বলছে অঘোর রায়ের ভাঁটার মতো দুটি চোখ। বাগানে ঢুকেই তিনি একলাফে গিয়ে ঘোড়াটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অশ্বদেহ দ্বিখন্ডিত করে সেই প্রচন্ড খড়ের কিয়দংশ মাটিতে ঢুকে গেল। রাজগন্ধার উজ্জ্বল লাল রক্তের ছোপ–সবুজ ফুল শাখায় বীভৎস ক্ষতের মতো রক্তের চাপ–অন্তঃপুরিকাদের অস্ফুট আর্তনাদ আর পাইক বরকন্দাজের শোরগোল সে এক বিকট দৃশ্য। কাঁপতে কাঁপতে অঘোর রায় হলেন ধরাশায়ী। তার পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। জমিদারে জমিদারে এ নিয়ে শুরু হলে প্রচন্ড বৈরিতা। মামলা-মোকদ্দমা আর ষড়যন্ত্রের বেড়াজালে বিপর্যস্ত হয়ে অঘোর রায় হলেন দেশত্যাগী। তারপর কালক্রমে রায়নগর রূপান্তরিত হল বায়নঘরে।
গ্রামটি মুসলমানপ্রধান–দু-দিকে মালীগাঁ আর থৈরকোলাতে হিন্দু প্রায় একজনও নেই। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে জীবনযাত্রার আদান-প্রদানের তাগিদে এমন একটি সহজ হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল যে, কেউ কাউকে পর মনে করত না। গ্রামসুবাদে বয়ঃকনিষ্ঠরা পরস্পর পরস্পরকে দাদা, পুতি (কাকা), ঠাকুরভাই প্রভৃতি বলে ডাকত। এর আসল কারণটা প্রধানত অর্থনৈতিক। জীবিকার ক্ষেত্রে একে অপরের সঙ্গে এতটা ঘনিষ্ঠ ছিল যে, জীবনেও তার প্রভাব আসতে বাধ্য। গ্রামের হিন্দুদের মধ্যে যারা কৃতী পুরুষ তাঁরা প্রায় সবাই থাকতেন বিদেশে। এঁদের জোতজমি চাষবাসের ভার ছিল মুসলমান প্রধানিয়াদের হাতে। তাঁরা হাল-লাঙল দিয়ে জমি চষতেন, ফসল তুলতেন। যাঁরা বাড়িতে থাকতেন তাঁদের অর্ধেক ফসল দিয়ে দিতেন। এমনও হয়েছে যে, জমির মালিক হয়তো চিঠি লিখেছেন–তাঁর প্রাপ্য ফসলের মূল্য মনিঅর্ডার করে পাঠাতে। মুসলমান বর্গাদার প্রধানিয়ারা কড়াক্রান্তি হিসেব করে টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন–কোথাও একবিন্দু ফাঁকি বা কারচুপি ছিল না। যেন মনে হত অলক্ষ্যে কোনো অদৃশ্য চক্ষু তাঁদের কারবার সব দেখছে–এমনি ধর্মভীরু আর নিরীহ ছিলেন তাঁরা। একটা নিশ্চিত বিশ্বাসের শক্ত জমিতে ছিল তাঁদের জীবনের ভিত, সদাসন্তুষ্ট কঠোর পরিশ্রমী আর নিরীহ ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দেখেছি হিন্দু প্রতিবেশীদের সঙ্গে কী অমায়িক আর প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করতে। আমার কাকা ছিলেন ডাক্তার। বাড়িতেই প্র্যাকটিস করতেন। সন্ধ্যাবেলায় তাঁর বৈঠকখানায় এসে জুটতেন একে একে হাজি বাড়ির বড়ো হাজি, উত্তরপাড়ার আকবর আলি, পাঞ্জৎ আলি, মুনশি গ্রামের প্রধানিয়ারা। গাছপিঁড়িতে বসে যেতেন এঁরা–মাটির মালসাতে (দেশে বলে ‘আইল্যা’) তুষের আগুন জিইয়ে রাখা হত টিকে ধরাবার জন্যে। গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলত বৈঠক, আর চলত ছিলিমের পর ছিলিম তামাক। যুদ্ধের সময়টা এখানে ভিড় হত বেশি। সবাই যেন শুনতে চায় আশার বাণী, আশ্বাসের বাণী- সবাই যেন প্রাণপণে বিশ্বাস করতে চায় এ দুর্দিনের অন্ত আছে। ডাক্তার কাকার কাছে তাই অনেকে ছুটে আসত, তাঁর কাছ থেকে সমর্থনের বাণী শুনবার জন্যে। কেউ খেতে পাচ্ছে না–রোগে ওষুধ নেই, পথ্য নেই, ডাক্তারকাকা তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বলিষ্ঠদেহ মুসলমান চাষিদের দেহে বুভুক্ষা আর অনাহারের ছাপ ব্যাণ্ডেজ খোলা পোড়া ঘায়ের মতো মুখে শুকনো হাসি–যেমন করুণ তেমনি বীভৎস। রাজনৈতিক আধি আর ঝোড়ো হাওয়ার অন্তরালে একটি সহজ সরল জীবনের সমতল ভূমিতে সবাই হাতে হাত মিলিয়ে চলত এখানে। আমাদের বাড়ির কিছুদূরেই ছিল হাজিবাড়ি। এ বংশের কোন পুরুষ কবে একবার মক্কা গিয়ে ‘হজ’ করে এসেছিলেন, তাই থেকে এরা সবাই হাজি’। বড়ো হাজির কথা আজ মনে পড়ে। মেহেদি রঙের দাড়ি আর চোখদুটিতে ছিল একটা সরল বিশ্বাসের ছাপ, চোখ এমন করে হাসতে জানে–একথা এর আগে আমার জানা ছিল না। শেষরাত্রে তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের ‘আজান আমাদের পাতলা ঘুমের আস্তরণ ভেদ করে কানে এসে বাজত। আমাদের ভালো কোনো খবর পেলে এই মুসলমান বৃদ্ধটি সত্যি সত্যি খুশি হতেন–প্রাণখোলা হাসির ছটায় মেহেদি রঙের দাড়িতে একটা আলোর ঝিলিক ঠিকরে পড়ত যেন।
টুকরো-টুকরো কত ছবি আজ মনে পড়ে! মনে পড়ে স্বরূপদাস সাধুর কথা। একটা জীর্ণ আলখাল্লা গায়ে-হাতে খঞ্জনি আর কাঁধে শতচ্ছিন্ন ভিক্ষার ঝুলি। কিন্তু মুখে নিশ্চিত প্রত্যয়ের কী অপূর্ব প্রশান্তি এক পা ঊর্ধ্বে খঞ্জনি বাজিয়ে সে গাইত, ।
এতদিন পরে ঘরে এলি রে রামধন,
মা বলে ডাকে না ভরত,
মুখ দেখে না শত্রুঘন-ন-ন।
তখন অনুতপ্তা কৈকেয়ীর মর্মজ্বালা যেন যুগযুগান্ত পেরিয়ে আমাদের মনের ভেতর ছুঁয়ে যেত। বাড়ির সবাই এসে জড়ো হয়েছে উঠোনে, স্বরূপদাস খঞ্জনি বাজিয়ে নেচে-নেচে গান গাইছে। বাড়ির কুকুরটা পর্যন্ত অবাক হয়ে দেখছে–মাঝে-মাঝে কান খাড়া করে বোধহয় গানও শুনছে। সকলে ফরমাশ করে যাচ্ছেন–স্বরূপদাস অক্লান্তভাবে গান গেয়ে চলেছে কখনো-বা দেহতত্ত্ব, কখনো-বা শ্যামাসংগীত, কখনো-বা কৃষ্ণ-রাধিকার বিরহ-মিলন-কথা। যাওয়ার সময় কয়েক মুঠো চাল, কারও দেওয়া কিছুটা ডাল এবং আনাজ ঝুলিতে পুরে গুনগুন করে চলে যেত স্বরূপদাস।
আমাদের গ্রামে সংকীর্তনের রেওয়াজ ছিল খুব বেশি। প্রতিসন্ধ্যাতেই কীর্তন হত। রমণী পালের হাত ছিল মৃদঙ্গের বোল ফোঁটাতে ওস্তাদ। সরু লিকলিকে চোহারা–চুলগুলি বড়ো বড়ো। কীর্তনের সময় মৃদঙ্গটি কাঁধে ঝুলিয়ে সে যেভাবে লাফাতে থাকত ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাতে আমরা অবাক হয়ে যেতাম। বড়ো-বড়ো চুলগুলি একবার এপাশে আর একবার ওপাশে কাত হয়ে পড়ছে, এক একবার এক-একটি প্রচন্ড লাফ দিয়ে সে যাচ্ছে ডান দিক। থেকে বাঁ-দিকে আর মৃদঙ্গের বোলে আওয়াজ উঠছে যেন গম্ভীর ওঙ্কারধ্বনির মতো। একবার জ্বরগায়ে অষ্টপ্রহর সংকীর্তনে মৃদঙ্গ বাজাতে গিয়ে রমণী পাল মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিল অস্নাত, অভুক্ত অবস্থায়। কিন্তু তবু সে মৃদঙ্গ ছাড়েনি। কিন্তু আজ–আজ সে রমণী পালের। কাঁধে আর মৃদঙ্গ নেই-শান-বাঁধানো শহর কলকাতার পথে-পথে সে আজ ফিরি করে ফিরছে।
এক সময় আমাদের গ্রামে ‘নিমাই সন্ন্যাস’ পালাকীর্তনের ঢেউ আসে। প্রথম পালাকীর্তনের অনুষ্ঠান হয় আমাদের বাড়িতে। উত্তরপাড়ার বংশী, খগেশ, নীরু, আবু–এসব ছেলেরা এতে অংশগ্রহণ করে। বলা বাহুল্য, সেদিন উত্তেজনা ছিল প্রচুর–আয়োজন ছিল না। সাজপোশাকের কোনো বালাই ছিল না। খগেশ নিমাই সন্ন্যাসের পালায় শ্রীরাধার ভূমিকায় অভিনয় করে। শুক-শারি এসে গাইছে,
ওঠ-ওঠ রাইশ
শীভোর হল অমানিশি
ও হরি! শ্রীমতী রাধিকা প্যান্ট পরেই সলজ্জ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে শুক-শারির প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন। কিন্তু সমস্ত দর্শকসমাজ এমনি অভিভূত হয়ে ছিল যে, এতে তাদের বিন্দুমাত্র রসবোধের ব্যাঘাত ঘটেনি।
শচীমাতার বিলাপে হিন্দু-মুসলমান সকলের চোখ সজল হয়ে ওঠে। ভোর হতেই পালা শেষ হয়ে বের হল প্রভাতফেরি। কাঁপা-কাঁপা, টানা-টানা সুরে সে কী গান–আমাদের বাড়ির দ্বাররক্ষী ছিল দুটো বড়ো তেঁতুল গাছও তল্লাটে এত প্রকান্ড গাছ আর ছিল না। তার চিকনচিকন পাতার ঝালর ছিঁড়ে সূর্যের আঁকাবাঁকা আলো এসে পড়ছে; আলো আর সুরে কী নেশাই না সেদিন লেগেছিল।
আমাদের গ্রাম থেকে কয়েক মাইল দক্ষিণে সাঁচার। সেখানকার রথযাত্রা’ আমাদের অঞ্চলে বিখ্যাত। প্রতিবছরই আমাদের বাড়ির নৌকা করে আমরা সবাই রথযাত্রায় যেতাম। সকাল সকাল খেয়ে-দেয়ে আমরা রওনা দিতাম। আশপাশে আরও কত নৌকা–কত দূরদেশ থেকে, কত ভিন গাঁ থেকে এরা আসছে। নৌকার ছইয়ের ওপর কারও কারও দেখছি জ্বালানি কাঠ বাঁধা–অর্থাৎ ২। ৩ দিন আগে থেকেই তারা রওনা দিয়েছে। রাস্তায় রাস্তায় বাজার বা গঞ্জে নৌকা ভিড়িয়ে তারা আহারপর্ব সমাধা করে।
জগন্নাথদেব দর্শন ও রথের রশি ছোঁয়া নিয়ে ধর্মভীরু যাত্রীদের সে কী উন্মত্ত উন্মাদনা! কারও জামা ছিঁড়ে গেছে, রথের রশির কাদায় সর্বাঙ্গ চিত্রবিচিত্র হয়ে উঠেছে, কিন্তু সেদিকে কারও লক্ষ নেই–মুখে শুধু ‘জয় জগন্নাথ’ ধ্বনি। অদূরে অপেক্ষমান মেয়েরা হুলুধ্বনি দিচ্ছেন, ক্রমাগত শঙ্খ-কাঁসর-ঘণ্টার আওয়াজ, নারীকন্ঠের হুলুধ্বনি জনতার জয়ধ্বনি মিলে মিশে একটি বিরাট শব্দস্তম্ভ রচনা করেছে যেন–চারিদিকে মানুষের কেবল মাথার সমুদ্র তার মধ্য দিয়ে চলেছে জগন্নাথের রথ। বিকেলের সূর্য তার ওপর আবির ছড়িয়ে দিচ্ছে মুঠোমুঠো। সে-দৃশ্য কি কখনো ভুলতে পারি?
রথযাত্রা শেষে যাত্রীদের বাড়ি ফেরার পালা। সন্ধ্যার অন্ধকার এসেছে ঘন হয়ে। নৌকায় নৌকায় সবাই ফিরছে–আর চারিদিকে খোঁজাখুঁজি চলছে যারা এখনও ফেরেনিঃ মাঝি তাদের হাঁক দিচ্ছে সন্ধ্যার শান্ত আবহাওয়ায় কাঁপা কাঁপা ঢেউ তুলে সে-ডাক আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। ছেলেরা কেউ সদ্য ক্রীত মেলার বাঁশিতে তুলেছে বিচিত্র বেসুরো আওয়াজ–কেউ ধরেছে গান।
এমনি কত কথা–কত ছবি আজ মনে পড়ে। কত কথা বলব আর কত ছবি আঁকব? বুকের পাঁজর খুলে দিতে কী ব্যথা তা কি কেউ কখনো বলে বোঝাতে পারে? হয়তো এমন দিন আসবে, যেদিন স্বরূপদাসের সেই গান–সেই গান গেয়ে কেউ আমাদের জন্যে এগিয়ে এসে বলবে,
এতদিন পরে ঘরে এলি রে রামধন,
মা বলে ডাকে না ভরত, মুখ দেখে না শত্রুঘন–
সেদিন কতদূরে?
.
চান্দিসকরা
বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে : আমাদের কপালে যা আছে তাই ঘটবে, কিন্তু তুমি এ অবস্থায় কিছুতেই গ্রামে এসো না।
চিঠি পড়ে মনটা কেঁদে উঠল। আমার বাড়ি, আমার গ্রাম, আজ তার দ্বার আমার কাছে রুদ্ধ। যে পথের ধূলি মিশে রয়েছে আমার অস্তিত্বের সঙ্গে, যে গ্রামের জল-কাদা, আলো বাতাস গায়ে মেখে জীবনের পথে এক এক পা করে এগিয়ে এসেছি–আজ সে-গ্রামে ফিরে যাওয়া আমার নিষেধ, সেখানে আমি নিরাপদ নই!
চিঠিখানা চোখের সামনে পড়ে রয়েছে। উর্দু আর ইংরেজিতে লেখা টিকিটের মাঝখানে পাকিস্তানি ‘ন্যায়পরায়ণতার’ তুলাদন্ড আঁকা–তার ওপরে জ্বলজ্বল করছে আমার গ্রামের ডাকঘরের ছাপ। এই ডাকঘরের ওপর কী বিরাট আকর্ষণ ছিল। ডাক আসবার একঘণ্টা আগে গিয়ে ডাকঘরে বসে থাকতাম-কলকাতা থেকে খবরের কাগজ আসবে, বিভিন্ন জায়গা থেকে বন্ধুদের চিঠি আসবে–সারাদিনের একঘেয়েমির ভেতর এটা ছিল মস্তবড়ো সান্ত্বনা। আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে রোজ বেলা দশটা-এগারোটার সময় ঝুনঝুন করে ঘণ্টা বাজিয়ে চলে যেত ডাক-হরকরা। ছেলেবেলায় সেই ঘণ্টার প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল। যেখানেই থাকতাম, হরকরার ঘণ্টা শুনলেই ছুটে এসে দাঁড়াতাম রাস্তার পাশে। দেখতাম হাঁটুর ওপরে লুঙ্গি পরে, একটা খাকি শার্ট গায়ে দিয়ে ধুলোমাখা খালি পায়ে, ডাকের ঝোলা কাঁধে নিয়ে ছুটে চলেছে হরকরা। কোনো কোনোদিন আমাদেরই পুকুরের শান-বাঁধানো ঘাটের পাশে, বকুল গাছের ছায়ায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ত। ঘাটের একটা সিঁড়িতে ঝোলা রেখে নেমে যেত জলের মধ্যে, মুখ-হাত ধুয়ে মাথায় জল দিয়ে আবার রওনা হত– কাঁধের ঝোলা থেকে শব্দ আসত, ঝুনঝুন, ঝুনঝুন। ভট্টাচার্য বাড়ির কাছ থেকেই ডাকঘরের রাস্তা গেছে বেঁকে–তারপর হরকরাকে আর দেখা যেত না। কিন্তু তার ঘণ্টার অনুরণন তখনও বাজত আমার কানে। আজও তেমনি করেই হয়তো হরকরা ছুটে চলেছে। তার ঘণ্টা বাজিয়ে–এ-চিঠিখানাও সে-ই বহন করে এনেছে। কিন্তু তার সেই ঘণ্টা শোনবার জন্যে আমি আর সেখানে নেই!
সপ্তাহে দু-বার করে আমাদের যে বিরাট হাট বসে তার মালিক আমরা। হাটের খাজনা আদায় করবার ভার পাঁচজন ইজারাদারের ওপর–তারা সকলেই মুসলমান। প্রতি হাটবারে কয়েক সহস্র লোক জড়ো হয় বেচা-কেনার জন্যে। ছেলেবেলায় আমাদের হাটে যাওয়া বারণ ছিল–পাছে হারিয়ে যাই এই ভয়ে। হাটে যাবার একটা বড়ড়া পথ ছিল আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে। সে পথের ধারে আমাদের পুকুর আর তার বাঁধানো ঘাট, সেই ঘাটে গিয়ে বসে থাকতুম। কত লোক হাটে যেত সে-পথ দিয়ে কেউ তরকারি নিয়ে, কেউ মনোহারি জিনিস নিয়ে, কেউ হাঁস-মুরগি নিয়ে, কেউ কাঠ-বাঁশ নিয়ে–এমনি কত সব দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে ওরা যেত। কুমোরপাড়া, তাঁতিপাড়া, কামারপাড়া ইত্যাদি অঞ্চলের শ্রমজীবী লোকেরা যেত তাদের নিজ নিজ জিনিস নিয়ে। বসে বসে আমরা দেখতুম। শেষবেলার দিকে ছুটত জেলেরা। দূর গাঙে ওরা চলে যেত মাছ ধরতে, তাই হাটে যেতে তাদের দেরি হত। মাছের ভারে নুয়ে পড়ত তাদের ইস্পাতের মতো দেহ, ঘামে নেয়ে উঠত প্রতিটি লোমকূপ। দৌড়ে দৌড়ে যেত ওরা–জেলেদের আস্তে হাঁটতে কখনো আমি দেখিনি। হাটের পথে যেতে যেতে কত কথা ওরা কইত–তার ভেতর রাজনীতি ছিল না, অর্থনীতি ছিল না, ঘরের কথা, দৈনন্দিন জীবনের ছোটোখাটো সুখ-দুঃখের কথা, আশা নিরাশার কথা–এ নিয়েই মন তাদের ভরে থাকত।
আগেই বলেছি আমাদের পুকুরের বাঁধানো ঘাটের দু-ধারে মস্তবড়ো দুটো বকুলগাছ। বকুল ফুল পড়ে ঘাটের চাতাল সকাল-সন্ধ্যায় সাদা হয়ে থাকত। তার মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে পড়ত বাড়ির অন্দরমহল পর্যন্ত। ঘাটের যে সিঁড়িগুলো জল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তাতে বসে গ্রামের ব্রাহ্মণরা আহ্নিক করত দু-বেলা। আর ওপরের বিস্তৃত চাতালে মুসলমানরা পড়ত নামাজ। হাটবারে ঘাটটাকে বিশেষ করে ঝাড় দিয়ে রাখা হত–কারণ সেদিন কয়েকশো লোক আমাদের ঘাটে আসত নামাজ পড়তে। এক সারিতে ৪০। ৫০ জন দাঁড়িয়ে যেত। সারিতে দাঁড়ানো এতগুলো লোকের একই সঙ্গে ওঠা-বসার ভেতর কেমন একটা ছন্দের দোলন ছিল, যা আমার খুব ভালো লাগত। প্রতিদিন এমনি দৃশ্য দেখতে দেখতে তার ছাপ চিরতরে পড়ে গেছে মনের পর্দায়, সারাজীবন গ্রামছাড়া থাকলেও আমি তা ভুলব না। আজও এ নিয়মের ব্যতিক্রম নিশ্চয়ই হয়নি, আজও তারা একইভাবে আল্লার উপাসনা করছে আমাদের ঘাটে কিন্তু পাশে বসে আহ্নিক করবার মতো কেউ হয়তো আর নেই!
হাটবারে যে দুটো লোককে সবচেয়ে বেশি করে মনে পড়ত তারা হচ্ছে আমিরউদ্দিন আর মাখখু মিয়া। ওরা ছিল আমাদের হাটের ইজারাদার। হাট ভেঙে যাবার পর আমাদের জন্যে চিনেবাদাম, ছোলাভাজা ইত্যাদি খাবার নিয়ে রাত্রিবেলায় ওরা আসত। শীতের সময় পেতাম বড়ো বড়ো কুল। বহু বছর আগে বড়দার সঙ্গে আমিরউদ্দিন এসেছিল কলকাতায়। কলকাতার মতো শহর যে পৃথিবীতে থাকতে পারে এ ছিল ওর কল্পনার বাইরে। শেয়ালদা থেকে পথে নেমে সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে রইল, বুঝতে পারল না সত্যি মাটির পৃথিবী, না রূপকথার স্বপ্নপুরী! কিন্তু তার পরের রাত্রিতেই আমিরউদ্দিন যা কান্ড করলে, তা ভেবে কতদিন আমরা হেসেছি। তখন রাত বারোটা কি একটা হবে–হঠাৎ ঝুপঝুপ করে করে বৃষ্টি নামল। তার আগের কয়েক মাস ভয়ানক খরা যাচ্ছিল–এতে ফসলেরও ক্ষতি হয়েছিল প্রচুর। বৃষ্টির আওয়াজ কানে আসতেই আমিরউদ্দিন ধড়মড় করে বিছানা থেকে উঠে পড়ল। দাদাকে ডেকে বললে, বাবু, কাইলই আঁই বাড়ি যামুগই। খোদার দোয়ায় বৃষ্টি অইল, খ্যাতে লাঙল ফেলাইতে না পাইল্লে, এ-খন্দে আর চাইল ঘরে তুইলতে পাইতাম না উবাস মরুম। আরে ইস্টিশনে নিয়া কাইল সকালেই গাড়িত তুলি দি আইয়েন, বাবু। অনেক বোঝানো সত্ত্বেও আর একদিনের জন্যেও কলকাতায় থাকতে রাজি হল না আমিরউদ্দিন। মাঠের ডাক এসেছিল তার জীবনে, লিকলিকে ধানের শিষের সোনালি স্বপ্নের কাছে কলকাতার ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে গেল।
সেদিন আমিরউদ্দিনের বোকামি দেখে হেসেছিলাম–আজ বুঝতে পারছি গ্রামের আকর্ষণ গ্রামের ছেলের কাছে প্রবল, কত গভীর। দিগন্তবিস্তৃত ধানখেতের স্বপ্ন কোনোদিন কি ভুলতে পারব? ধান কাটা সারা হবার পর শুরু হত আমাদের ঘুড়ি ওড়ানোর পালা। কত ধুলো গায়ে মেখেছি, দৌড়তে গিয়ে কতবার হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছি–কত রক্ত মাঠের ধূলির সঙ্গে মিশে রয়েছে। সেই মাঠ পেরিয়ে দুপুরের খাঁ খাঁ রোদে বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে যেতাম মনুমিয়ার বাড়ি। মনুমিয়া আখের চাষ করত, তার ওপর ছিল আমাদের লোভ!
রেজ্জাক মিয়ার খেজুরের রসও কি আমাদের কম প্রিয় ছিল! রাত্রে রস পড়ে হাঁড়ি ভরতি হয়ে থাকত সকালে সে-রস বিক্রির জন্যে পাঠানো হত গ্রামের বাড়িতে বাড়িতে। আমাদের বাড়িতেও খেজুরের রস কেনা হত পায়েস বানাবার জন্যে। আমাদের মন কিন্তু তাতে ভরত না। রেজ্জাক মিয়া ভোরবেলা যখন গাছ থেকে রসের হাঁড়ি নামাত, আমরা গিয়ে গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকতাম। আমাদের লোলুপ দৃষ্টি দেখে রেজ্জাক মিয়া কিছু রস আমাদের মধ্যেই বিলিয়ে দিত।
ঘটা করে দুর্গাপুজো হত আমাদের বাড়িতে। পুজোর কটা দিন লোকজনের ভিড়ে সারাবাড়ি গমগম করত। পুজো উপলক্ষ্যে একদিন স্থানীয় বিশিষ্ট মুসলমান ভদ্রলোকদের
নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো হত। পুজোর প্রসাদ তাঁরা খেতেন না, তাই তাঁদের জন্যে বন্দোবস্ত করা হত আলাদা খাবারের। পুজোমন্ডপের পাশেই আমাদের বৈঠকখানা ঘর। বিরাট আলোর ঝাড়ের তলায় পরিষ্কার চাদর আর তাকিয়া দিয়ে ফরাস পাতা হত। সকলে বসতেন সেখানে। আমরা ভয়ে বৈঠকখানা ঘরে ঢুকতাম না–আশপাশে ঘুরঘুর করে বেড়াতাম। আশরাফউদ্দিন, সোনা মিয়া, কালা মিয়া প্রভৃতি সকলেই হলেন গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তি। বহুকাল থেকেই আমাদের বাড়ির সঙ্গে নিবিড় ঘনিষ্ঠতা এঁদের। আমাদের পূর্বপুরুষের সম্পর্কে কত গল্প শুনেছি এঁদের মুখ থেকে। পুজোর সময় জিনিসপত্র জোগাড় করে দেবার ভার থাকত এঁদের ওপর–কোন জিনিস কত পরিমাণ প্রয়োজন এঁরা সব জানতেন। এঁরা সকলেই চাষি–কিন্তু গুরুজনদের মতোই এঁদের আমরা সমীহ করে চলতাম। ভালোবেসে এঁরা আমাদের কচি মন জয় করেছিলেন।
এমনি কত শত সাধারণ দৈনন্দিন স্মৃতি আজ ভিড় করে দাঁড়িয়েছে মনের দ্বারে। ছেড়ে আসা গ্রামের ফেলে-আসা দিনগুলো জীবন্ত হয়ে উঠছে আমার অন্তরলোকে। এদের কোনোটিই বিশেষ ঘটনা নয়–অতিসহজ-সরল, সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি কান্নার কথা। একদিন এর তেমন কোনো মূল্যই হয়তো আমার কাছে ছিল না, কিন্তু আজ তাকে হারিয়েছি, তাই সে হয়ে উঠেছে অমূল্য। একই গ্রামবাসী হিসেবে যুগ যুগ ধরে আমরা হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি বাস করে এসেছি–শুধু ধর্মবিশ্বাস ছাড়া আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও চিন্তাধারার ভেতর আর কোনো তফাতই ছিল না। দেশে যখন সমৃদ্ধি এসেছে, হিন্দু-মুসলমানের জন্যে সমানভাবেই এসেছে। যখন বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারীর তান্ডব শুরু হয়েছে, তখনও হিন্দু-মুসলমানের জীবনে সমানভাবেই পড়েছে তার অভিশাপ। কিন্তু কোন এক অশুভ মুহূর্তে ঘোষণা করা হল : হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের শত্রু, এদের ভেতর কখনোই মিল হওয়া সম্ভব নয়। মুসলমান প্রতিবেশী নতুন চোখে তাকাল হিন্দু-প্রতিবেশীর দিকে। বললে, তুমি আমার শত্রু–এতদিন যে আমরা পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে বাস করে এসেছি, তা মিথ্যে– এতদিন যে বন্ধুর মতো, ভাইয়ের মতো ব্যবহার করেছি, তাও মিথ্যে –শত শত বছর ধরে তোমাতে আমাতে যে আন্তরিকতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, তা কখনো সত্যি নয়! যে শত্রুতা হিন্দু-মুসলমানের ভেতর কোনোদিন ছিল না, দিনের পর দিন ধরে বিষাক্ত প্রচারের ফলে সে-শত্রুতা সৃষ্টি করা হয়েছে শুধুমাত্র একটি দুষ্ট রাজনৈতিক চক্রান্ত সফল করবার জন্যে।
সফল হয়েছে সে-চক্রান্ত। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ছল চাতুরির দ্বারা দেশকে করা হয়েছে দ্বিখন্ডিত। হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক ঐক্য, রাজনৈতিক ঐক্য, ভাব-ভাষা, চিন্তা-কল্পনা-সুখ দুঃখ হাসি-কান্নার ঐক্য নির্মমভাবে হার মানল ধর্মবিশ্বাসের অনৈক্যের কাছে। একটা জাতির জীবনে এর চেয়ে বড়ো অভিশাপ আর বোধহয় হতে পারে না। লক্ষ লক্ষ মুসলমানের লক্ষ লক্ষ প্রতিবেশী আমরা আজ হলাম ঘরছাড়া, দেশছাড়া!
কিন্তু এই ভৌগোলিক অস্ত্রোপচার আমাদের মনের নিবিড় ঐক্যকেও কি স্পর্শ করতে পেরেছে? না–পারেনি। কলকাতার নিষ্ঠুর নির্মম পরিবেশের মধ্যে মনের শান্তি কোনোদিন আমাদের আসবে না, আসতে পারে না। কলকাতার আকাশ-বাতাস, আলো-আঁধার, জল মাটি, গাছপালার সঙ্গে আমার গ্রামের প্রকৃতির তফাত, বৈজ্ঞানিকের চোখে হয়তো নেই, কিন্তু যে আলোতে প্রথম আমি চোখ মেলেছি, যে মাটি আমাকে বক্ষে ধরেছে, যে বাতাস ঘোষণা করেছে আমার জন্মবার্তা–তাকে আমি কেমন করে ভুলব, তার স্পর্শ যে আমার অস্তিত্বের অণুতে-অণুতে মিশে রয়েছে। আমার গ্রামের প্রতিটি ধূলিকণা, প্রতিটি জলবিন্দু, প্রতিটি লতাগুল্মের সঙ্গে আমার নাড়ির যোগ। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের সঙ্গে আমার অন্তরের বাঁধন-একটা কলমের আঁচড়ে সে সবই কি মিথ্যে হয়ে গেল!
আমরা বাস্তুহারা, শরণার্থী–ভারতের দুয়ারে ভিক্ষাপ্রার্থী : এই আমাদের একমাত্র পরিচয় আজ। এই পরিচয়ের রক্তাক্ত টিকা ললাটে এঁকে কলকাতার পাষাণ-দুর্গের নিষ্ঠুর বন্ধনের মাঝখানে বসে আমি আজ অশান্ত মনে চেয়ে রয়েছি আমার ছেড়ে-আসা গ্রামের দিকে।
রঘুনন্দন পাহাড়ের গা ঘেঁষে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত যে বিরাট ট্রাংক রোড চলে গেছে, তারই একধারে ত্রিপুরা জেলার দক্ষিণ প্রান্তে, কুমিল্লা সদরের অন্তর্গত আমার গ্রাম। নাম তার চান্দিসকরা। শুনেছি এককালে আমাদের গ্রামের নাম ছিল ‘চন্দ্র-হাস্য-করা, চান্দিসকরা তার সংক্ষিপ্ত রূপ। চান্দিসকরার আকাশ জুড়ে আজও চাঁদ হাসছে, প্রকৃতির সাজ বদল ঋতুতে ঋতুতে যথানিয়মেই চলেছে,বকুল ফুল পড়ে সাদা হয়ে যাচ্ছে আমাদের বাঁধানো ঘাট, চাঁপা-টগর-রজনীগন্ধা-হাসুহানা-ডুইচাঁপার গন্ধে ভোরের বাতাস আজও চঞ্চল হয়ে উঠছে, আম-কাঁঠাল-জাম-জামরুলের ভারে গাছগুলো নুয়ে পড়ছে,-মাছের তান্ডবে অশান্ত হয়ে উঠছে দিঘির কালো জল, কালবৈশাখীর প্রলয় নাচন শুরু হয়ে গেছে আকাশে-বাতাসে– মুসলমান চাষিরা দিন গুনছে মেঘের আশায়, কবে বৃষ্টি হবে, কবে খেতে লাঙল পড়বে : এসব আমি আজ দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তাঁতি-পাড়ার তাঁত আজ আর চলছে না, কুমোরের চাকা ঘুরছে না, কামারের লোহা জ্বলছে না, ছুতোরের বাটালি আজ নিস্তব্ধ! পৈতৃক ভিটা, পৈতৃক পেশার মায়া ত্যাগ করে তারা আজ দলে দলে হারিয়ে যাচ্ছে পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর ভিড়ের ভেতর। আমিও তাদেরই সগোত্র–চলতে চলতে ভাবছি : উলটো রথের পালা আসবে কবে?
.
বালিয়া
নিশুতি রাত…কৃষ্ণাচতুর্দশীর সূচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্য দিয়ে অতিসন্তর্পণে এগিয়ে চলেছে। আমাদের নৌকাখানি। নৌকার ছই-এর-দু-দিকই আবৃত… সম্মুখভাগে বসে আপন মনে গান গাইছে প্রতিবেশী কাসেম ভুইঞা..পেছন থেকে লগি দিয়ে নৌকা বেয়ে চলেছে যামিনী টিপরা। ছই-এর ভেতরে আমরা চারটি প্রাণী। সারাদিনের দারুণ অশান্তি আর উত্তেজনায় অবসন্ন! সর্বোপরি বর্তমানে জীবন পর্যন্ত সংশয়। কোনোক্রমে শহরে গিয়ে পৌঁছোতে না পারলে রাত্রিশেষে নররূপী পশুদের হামলা অবশ্যম্ভাবী–দিনের বেলায় গ্রামের মেয়েদের, বুড়োদের এবং শিশুদের শহরের নিরাপদ আস্তানায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। এ অঞ্চলে আমরা শুধু ছিলাম রাত্রির অবস্থা দেখে তারপর একটা চূড়ান্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করব বলে। কিন্তু গোধূলির ধূলি উড়বার সঙ্গে সঙ্গেই গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে দলবদ্ধভাবে আক্রমণ, লুণ্ঠন ও জখমের সংবাদ এল-প্রান্তীয় বড়ো সড়ক ধরে মশালের সাহায্যে হামলাকারীর দল হই-হল্লা করতে করতে এগিয়ে চলেছে,–কোথাও-বা সারি সারি নৌকার সাহায্যে ওরা অন্তর্বর্তী বিল জলা প্রভৃতি পার হয়ে একের পর এক বাড়িতে হানা দিচ্ছে। এসব দৃশ্য আমাদের বাড়ির পূর্ব দিকের রাস্তায় দাঁড়িয়েই দেখা গেল। অবশেষে ওপাড়ার রহমন খাঁ এসে যখন জানাল রাত্রিতে আমাদের বাড়ি আক্রমণের প্ল্যান হয়েছে এবং চারদিকের আবহাওয়া বাগে এনে সর্বশেষে গ্রাম-কেন্দ্রের এই শক্ত ঘাঁটিটিকে বিপর্যস্ত করাই তাদের অভিপ্রায়–তখন আমাদের সম্মুখে নিরস্ত্রভাবে নিশ্চিত মৃত্যুবরণ কিংবা আত্মরক্ষার জন্যে আত্মগোপন এ দুটির একটি পথ শুধু খোলা রইল। রহমান জানাল, আমাদের বাড়িতে সম্প্রতি যে কয়েকটি বড়ো বড়ো বাক্স-প্যাঁটরা আমদানি করা হয়েছে তাতে বহু অস্ত্রশস্ত্র ছিল বলে ওদের বিশ্বাস,–তাই শক্তি পুরোদস্তুর সংগ্রহ করে তবেই ওরা এখানটায় হানা দেবে এবং সেটা এ রাত্রেই! কিন্তু ওদের বিশ্বাস বা সাময়িক ভয়ের কারণ যাই হোক, শূন্য বাক্স-প্যাঁটরা এবং নিছক বাঁশের লাঠির ওপর ভরসা করে আমরা চারিটি প্রাণী সহস্রাধিক ক্ষিপ্ত পশুর সম্মুখীন হবার সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি। রাত্রিও প্রায় শেষ–অগত্যা কৌশলে পথের সুরক্ষিত ঘাঁটি পার হয়ে শহরে গিয়ে প্রাণ বাঁচানার পন্থাই সাব্যস্ত হল। প্রতিবেশী কাসেম খাঁর মস্তিষ্কের সুস্থিরতার কোনো প্রমাণই কোনোদিন পাইনি। আজ হঠাৎ এরকম দুঃসময়ে সে-ই অগ্রণী হয়ে এসে আমাদের নিরাপদে ঘাঁটি পার করে দেবার দায়িত্ব নিয়ে সত্যি অবাক করে দিল।
নৌকাঘাট ছেড়ে মাইলটাক দূরে ওদের ঘাঁটি। খালের এপারে-ওপারে ছাউনি ফেলে শিবির তৈরি করা হয়েছে। যেন একটি কাফেরও বিনাক্লেশে গ্রাম থেকে বেরিয়ে যেতে না পারে। দুপুরের দিকটায় এদের হাতেই ঘোষেদের বাড়ির নৌকাবোঝাই যাবতীয় মালপত্র লুষ্ঠিত হয়েছে, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে নৌকার যাত্রীদের যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা করা হয়েছে।
কে যায়?–মেজাজি স্বরে প্রশ্ন আসে একটা ছাউনির মুখ থেকে।
আমি কাসেম ভূঁইঞা।–কে রে? ইসমাইল নিহি?-কাসেম গান থামিয়ে ওদের প্রশ্নের জবাব দেয় এবং নিতান্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠে প্রতি-প্রশ্ন করে।
আরে এত রাত্রে যাচ কই?–কাসেমের উত্তর : কই আর যামু,–যাই–রাইত পোয়াইলেই ত প্যাটের চিন্তা,–তার ব্যবস্থার লাইগ্যা।
কাসেমের ব্যাবসা দুধ বিক্রি। গৃহস্থ বাড়ির দুধ দাদন দিয়ে দীর্ঘকালীন বন্দোবস্ত নেয়, প্রত্যহ ভোরে তাই বাড়ি থেকে সংগ্রহ করে শহরের মিষ্টির দোকানগুলিতে সে চালান দেয়। কাসেমের জবাবে ওরা সন্তুষ্ট হল, তাই আমাদের নৌকাও অবাধে বেরিয়ে এল সামনের দিকে।
এমনি করে সর্বনাশা ছেচল্লিশের এক নিশীথ রাত্রে মহাঅপরাধীর মতো নিজের পরমপ্রিয় পুণ্যতীর্থ জন্মভূমি, জন্মগ্রাম থেকে নিঃশব্দে বিদায় নিয়ে এলাম।… তারপর বছরের পর বছর কেটে গেছে–কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও সে-মাটির কথা ভুলতে পারিনি। আজন্ম যার আলো হাওয়া আমার জীবনকে বর্ধিত করেছে, যার মাঠ-ঘাট-বাট-বন অনুক্ষণ প্রভাবিত করেছে আমার মন, জ্ঞানোন্মেষের পর থেকে যাকে কেন্দ্র করে দীর্ঘ পঁচিশ বছরের অসংখ্য ঘটনা স্মৃতির ভান্ডার করেছে সমৃদ্ধ, মুহূর্তের তরেও তাকে ভুলি কী করে? আজও প্রতিমুহূর্তেই তাই শুধু পিছু-ডাক।
পূর্ববঙ্গের ভয়ংকর নদী মেঘনা। তারই পূর্বপারে অবস্থিত সুবৃহৎ রেল ও স্টিমার জংশন, বাণিজ্যবহুল বন্দর চাঁদপুর। আসামের কুলিধর্মঘটকে কেন্দ্র করে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে চাঁদপুরের ঐতিহাসিক আন্দোলন, জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম ও সংগঠনকর্মে উৎসর্গীকৃত প্রাণ ভারতের প্রবীণতম, সর্বজনশ্রদ্ধেয় জননেতাদের অন্যতম হরদয়াল নাগের কর্মসাধনা চাঁদপুরের পরিচয়কে ভারতের দূরতম প্রান্ত অবধি প্রসারিত করেছে। নতুন বাজার, খেয়া পার হলেই কয়েকটি পাটের কল, তার গা ঘেঁষে এঁকে বেঁকে রাস্তা চলেছে দক্ষিণমুখী, খানিকটা নীচু জমির হাঁটাপথ ছাড়িয়েই জেলা বোর্ডের বড়ো সড়ক সোজা চলে গেছে পূর্বে ও দক্ষিণে…এমনি চলতে চলতে শহরের কোলাহল যখন নিঃশেষে বিলীন হয়ে যায় যখন প্রায় দু-ক্রোশ পথ পড়ে গেছে পেছনে, সামনে তখন ছায়ায় ঢাকা, পূর্বে ও পশ্চিমে, উত্তরে ও দক্ষিণে বৃক্ষরাজির আবেষ্টনীর মধ্যে ছায়াছবির মতো চোখে পড়ে একটি গ্রাম–’বালিয়া’ : লৌকিক নাম ‘বাইলা। আধুনিক সভ্যতা নিয়ে গর্ব করবার মতো কিছুই তার নেই, কিন্তু প্রকৃতির অফুরন্ত, অজস্র আশীর্বাদ যে তাকে অনুক্ষণ ঘিরে রেখেছে, গ্রামের সীমানায় পা। দিতেই যেকোনো পথিকের তা চোখে পড়ে। গ্রামটির প্রবীণতার সাক্ষ্য আর প্রতিক্ষণের জাগ্রত প্রহরীরূপেই যেন দাঁড়িয়ে আছে একটি সুউচ্চ তালগাছ আর তার পাশে জোড়া আমগাছ-গ্রামের ঠিক হৃদপিন্ডের ওপর,-সেনদের বাড়ির একেবারে সামনেটায়। জমিদার হিসেবে নয়, শিক্ষায় ও সামাজিক মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠ হয়েই এই বাড়ি দূরাতীত থেকে সসম্মান দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে প্রতিবেশী গ্রামগুলোর।
আমাদের বাড়ি বরাবর গ্রামের সমুখে সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর, কোথাও উঁচু গাছপালা সূর্যদেবের আত্মপ্রকাশের পথকে অবরুদ্ধ করে রাখেনি। তাই প্রভাতের স্নিগ্ধতা আর সূর্যালোক মিলিয়ে যে দুর্লভ মাধুর্য প্রকৃতিদেবী দু-হাতে বিলাতে শুরু করেন, তার সম্মোহনে দলে দলে ছেলে মেয়ে ভিড় জমায় সেই আমগাছের তলায়; গাছের নবোদগত আম্রমুকুলে ঢিল ছোড়ে কেউ, কেউ বা অদূরে খালের হাঁটুজলে নেমে হাতমুখ প্রক্ষালন করতে থাকে।
চাঁদপুর জংশনে মেঘনা থেকে যে শাখা-নদীটি শহরটিকে দু-ভাগে ভাগ করে দিয়ে এগিয়ে গেছে সম্মুখপানে,–প্রায় সহস্র গজ পরেই তার রূপান্তর ঘটেছে প্রকান্ড খালে, ক্রমে আরও সংকীর্ণ হয়ে এই খাল বাণিজ্যবাহী জলপথরূপে শহরের সঙ্গে সহস্রাধিক গ্রামকে সংযুক্ত করে নোয়াখালির প্রান্তসীমায় গিয়ে মিশেছে। বর্ষায় তাই বাড়ির সম্মুখ দিয়ে সারি সারি চলমান নৌকার মজা দেখতে সকাল সন্ধ্যায় ছোটোদের ভিড় জমে, বড়োদের মধ্যে যাঁরা বিদেশবাসী, গাঁয়ে এসেছেন ছুটি-ছাটা উপলক্ষ্যে, খালের পাড়ে এখানে সেখানে দু-জন চারজন করে দল বেঁধে পলিটিক্স চর্চা করছেন তাঁরা। জিন্না বড়ো পলিটিশিয়ান কি গান্ধি বড়ো, সূর্য সেন-অনন্ত সিং-এর আমলই ছিল ভালো কিংবা সত্যাগ্রহই এনে দেবে বাঞ্ছিত স্বাধীনতা, পড়য়া হাল পটিশিয়ানদের মধ্যে তাই নিয়ে চলে অফুরন্ত বাক-বিনিময়।
…এই মাঝি, নৌকা থামাও। হঠাৎ হরিমোহন পরামানিক খালের পাড় দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে একরকম খালের জলে নেমেই একটা নৌকার ছই শক্ত হাতে টেনে ধরে।
কী অইল বাবু?–ছই-এর ওপর থেকে সশঙ্ক হয়ে প্রশ্ন করে মাল্লা আর পেছন থেকে মাঝি একই সঙ্গে।
কী অইল? মাঠের মধ্য দিয়া পাল তুইল্যা যাইতেছ, জানো না পাল তুইল্যা গেলে হেই জমিতে আর কোনোদিন ফসল অয়না?
ও হো,–এই নামা-নামা, পাল নামা।–মাঝির নিজেরও হয়তো চাষবাস আছে, তাই শস্যক্ষতির আশঙ্কাটা তার মনে সহজেই প্রবল নাড়া দেয়।
বর্ষার নতুন জলে খালে মাছ ধরার কী আনন্দ! পুঁটি, ট্যাংরা, বাতাসি আর কাজলী-বজরীর ঝাঁকিজালের ফাঁকিতে না পড়ে উপায় কী? জোছনা রাতে চাঁদা মাছগুলো চাঁদের আলোকে ঝিকমিক করে ওঠে জালের ফাঁকে ফাঁকে। অমাবস্যায় পাকা ধরুয়াদের হাত যেন অবলীলাক্রমেই অন্ধকারের মধ্যে জাল থেকে রকমারি মাছগুলোকে খুলে নেয়-কাঁটার ঘা লাগে না। প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় কালবৈশাখীর দৌরাত্ম্য। তারই মধ্যে বেপরোয়া হয়ে মাছ ধরা চলে,–মাঝে মাঝে কেবল কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে একজন অপরজনের অবস্থিতি জেনে নেয়।
সন্ধ্যা হতে-না-হতেই পাড়ায় পাড়ায় শিশুদের কাঁসর-ঘণ্টাধ্বনি আর অবিশ্রান্ত কলরব মুখরিত করে তোলে গ্রাম। মাঝে মাঝে খোল-করতাল নিয়ে দল বেঁধে এপাড়া থেকে ওপাড়া, এবাড়ি থেকে ওবাড়ি। আমাদের গ্রাম-পরিবেশের এ ছিল এক আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।
মাঝে মাঝে পালা সংকীর্তনের আসর জমে উঠত আমাদের বাড়িতে কিংবা আমাদের জ্ঞাতিবাড়ি পশ্চিমের বাড়িতে। গাইয়ে–’বাইলার দল’! আমাদের গ্রাম ও প্রতিবেশী গ্রামের প্রায় দু-ডজন কীর্তনীয়া আর কীর্তন-রসিক নিয়ে গড়া এইদল। বছর পাঁচ পুরোদস্তুর ট্রেনিং দিয়ে এরা সত্যিকারের একটা ভালো দল খাড়া করেছে।–’রাধার বিচ্ছেদ’ ‘নিমাই-সন্ন্যাস, ‘মানভঞ্জন’, ‘লক্ষ্মণের শক্তিশেল’, ‘নৌকাবিলাস’–প্রতিটি পালাগানের যেমন মর্মস্পর্শী রচনা, তেমনই তার সুর।
পুবের হিস্যার সোনাদার বার্ষিক শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছে, সন্ধ্যায় পালাকীর্তনের ব্যবস্থা। ত্রিপল টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে বিরাট উঠোনের ওপর। বসবার ঠাঁই শতরঞ্চি আর মাদুর ইতিমধ্যেই শ্রোতৃসমাগমে ভরে গেছে। তা ছাড়া একপাশে গাছপিঁড়িতে অত্যন্ত আগ্রহভরে বসে আছেন আমাদের অশীতিপর বৃদ্ধ প্রতিবেশী ও প্রজা মেহেরুল্লা খাঁ এবং তাঁর আশপাশে ইসমাইল শেখ, হরমোহন খাঁ, হামির ভুইঞা, ইয়াসিন গাজি, কলন্তর খাঁ, রহমান এবং আরও বহু মুসলমান। ফরমায়েশ হল, ‘নিমাই সন্ন্যাস’ হোক!
দলপতি জগদীশ চন্দ আর রমেশ নাহা, মূল গায়েন হরিচরণ মহানন্দ, বায়েন (খোল বাজিয়ে) বিভূতিদা, ওরফে বিভূতি পাগলা, দোহারদের মধ্যে প্রধান অনন্ত আর শিশির কাকা–কালু, ব্রজেন্দ্ৰকাকা, ছোট্টকাকা এঁরা দ্বিতীয় পঙক্তির। আর একজন আছেন চিত্তদা। তিনি ক্ষীণদৃষ্টি, সত্যি কোনোদিন কোনো গান গেয়েছেন কি না সঠিক কেউ বলতে পারে না। তাহলেও কথা এবং সুরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখভঙ্গি অব্যর্থরূপে প্রমাণ করে তাঁর কীর্তনপ্রিয়তার কথা। আসলে কীর্তনপ্রিয়তাও তত বড়ো কথা নয়, যত বড়ো কথা হচ্ছে দলের লিষ্টিতে নাম রাখা! তবে চিত্তদা কিন্তু গল্পরসিক। শুধু রসিক নন, গল্পস্রষ্টা! বারোহাত কাঁকুড়ের তেরোহাত বিচি আর তিলকে তাল করার অসংখ্য গল্প মুহূর্তে বানিয়ে গানের ফাঁকে ফাঁকে আসর জমাতে তাঁর জুড়ি নেই! হরিচরণ হাতের করতালসহ হাত দুটি তুলে সভ্যগণ’ সমীপে নমস্কার জানিয়ে শুরু করে,
বাছা নিমাইরে,–বাছা নিমাই,
কোথায় গেলি রে,
দুঃখিনী মায়েরে ফেলে!
কণ্ঠ যেমন তীক্ষ্ণ, তেমনি মধুর। প্রধান দোহার অনন্তও মোটেই ‘ফ্যালনা’ নয়। ওদিকে বায়েন বিভূতি পাগলা এ তল্লাটের ওস্তাদ খোল বাজিয়ে। তাঁর খোল সত্যিই কথা কয়–আর এই খোল সহরতে তার নৃত্যের অপূর্ব ভঙ্গিমা বাইলার দলের প্রধান আকর্ষণ। উপযুক্ত সঙ্গতের মধ্যে গান সহজেই জমে ওঠে। দ্রুততালে তখন গানের অপর একটি কলি গাওয়া হচ্ছে,
নিমাই তোরে কোলে লব,
সব দুঃখ পাশরিব,
বড়ো আশা করেছিলাম মনে–
নিমাই রে!
গান শুনতে শুনতে পুত্রশোকে শোকাতুরা দক্ষিণহিস্যার মণিদি সুরের মূর্ঘনায় মূৰ্ছিতা হয়ে পড়ে! তাঁকে নিয়ে উদব্যস্ত হয়ে ওঠেন মেয়েরা। গান চলতেই থাকে। গায়েন, বায়েন, দোহার, শ্রোতা কেউ যে তখন আর এ জগতে নেই! অদ্ভুত অপূর্ব রসানুভূতি– আজও যার রোমাঞ্চ জাগে দেহে ও মনে।
সেনদের বাড়ির দোলউৎসব সুবিখ্যাত। সর্বজনীনতার মাধুর্য দিয়ে মন্ডিত এ উৎসবের প্রতিটি অঙ্গ। গ্রামের সবাই, এমনকী আশপাশের গ্রামেরও বহু ছেলে-বুড়ো বর্ষঘুরে আসতেই এ উৎসবের প্রত্যাশায় দিন গুনে চলে। পুজোর আনন্দ, আবিরের ছড়াছড়ি তো আছেই–তা ছাড়াও অষ্টপ্রহর সংকীর্তনান্তে মহোৎসবের খিচুড়ি আর লাবড়া! সেদিন সারদা পিসি এসে ধরে পড়লেন উদ্যোক্তাদের–তাঁর গুরুঠাকুর এসেছেন, মহোৎসবের পর তাঁকে দিয়ে শ্রীশ্রীগীতা পাঠ করাতে হবে। অতিউত্তম প্রস্তাব, মুহূর্তে পশ্চিম হিস্যার বাঁধানো বারান্দায় একটা বেদির মতো তৈরি করে দেওয়া হল, তার ওপরে বসলেন পন্ডিত কমলাকান্ত কাব্যতীর্থ। সুপুষ্ট বলিষ্ঠ দেহ, গৌরকান্তি, মুখাবয়বে জ্ঞান-গভীরতার ছাপ সুস্পষ্ট। মেয়েদের মঙ্গলশঙ্খধ্বনির পর তাঁর গুরুগম্ভীর কণ্ঠ থেকে ধ্যানমন্ত্র উচ্চারিত হতে থাকে,
মূকং করোতি বাঁচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম
যকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম।
তারপর বেছে বেছে কয়েকটি শ্লোক পাঠ আর বাংলায় তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন পন্ডিতমশায়। শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শোনে অমৃতময়ী শ্রীভগবানবাণী-সারগর্ভ জীবনদর্শনের মধুর ব্যাখ্যান। হঠাৎ টিপরার ‘জুম’ সর্দার কৈলাস সভায় ছুটে এসে ডুকরে কেঁদে ওঠে –’আমার জোয়ান মর্দ ছেলেটি তিন দিনের জ্বরে মারা গেল!’ সভাস্থল থেকে একটা তীব্র বেদনার ধ্বনি উত্থিত হয়। বিভূতিদা, যামিনীকাকা ও আমরা জনকয়েক মিলে কৈলাসকে সান্ত্বনা দিতে দিতে নিয়ে যাই স্থানান্তরে, কেউ কেউ লেগে যায় শ্যামমোহনের সৎকারের ব্যবস্থায়।
এ অঞ্চলে অনেক টিপরার বাস। চেহারায় টিপরাদের ত্রিপুরা রাজ্যের রাজাদের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে, তাই ওরা ত্রিপুরার আদিম অধিবাসী বলে দাবি করে। ফরসা রং ছাড়া কালো রং একজনেরও নেই ওদের মধ্যে, অদ্ভুত শক্ত বাঁধন দেহের, যেন লোহা পিটিয়ে গড়া হয়েছে। যতদূর জানা যায়, আমাদের পূর্বপুরুষগণ এদের প্রজাস্বত্ব দিয়ে এনেছিলেন গ্রামরক্ষী ও বিশ্বাসী অনুচররূপে। এদের সকলের পদবিই ‘সিং’-কৈলাস সিং, মিষ্ট সিং, যামিনী সিং, রমণী সিং, কামিনী সিং, এমনি সব নাম। মেয়েরাও পুরুষদের মতো সমান পরিশ্রমী ও বিনয়ী। সাধারণত ওরা কয়েকটি পরিবার দল বেঁধে একজায়গায় ছোটো ছোটো কুঁড়ের মধ্যে বাস করে। এই বাস-ব্যবস্থাকেই বলা হয় ‘জুম’। প্রায় প্রত্যহই বিকেলের দিকে আমরা বেড়াতে যেতাম কোনো-না কোনো জুমে। টিপরাদের সঙ্গে আলাপে অফুরন্ত আনন্দ পেতাম। ওদের সরলতা, সৎসাহস, আতিথেয়তার কথা আজ বড়ো বেশি করে মনে পড়ে।
এগ্রামে অধিকাংশই টিনের ঘর। পাকা ঘর শুধু একটি–আমার খুল্লতাত তার মালিক। দোতলা দালান, দক্ষিণ খোলা, অবিশ্রান্ত হাওয়ার আনাগোনা, তারই লোভে সন্ধ্যার দিকে ছেলে-বুড়ো জমায়েত হয় কাকার শান-বাঁধানো বারান্দায়। আজগুবি গল্পে জমে ওঠে ভরা বৈঠক। প্রধান গল্পকার এবাড়ির অর্ধশতাব্দীর পুরাতন ভৃত্য সুধন্য। এমনি সময় যথারীতি ডাক পড়ে কবিয়াল গৌরাঙ্গের–বৃদ্ধ দীনদয়ালের বড়ো ছেলের। গৌরাঙ্গ আমাদের দু-বাড়ির কোনো-না-কোনো হিস্যার কাজে আছেই, যদিও কেবল খোরাকি দিয়েও কোনো এক হিস্যা তাকে একনাগাড়ে দীর্ঘদিন রাখতে নারাজ। গৌরাঙ্গের পৈটিক দাবিটা বড়ো মাত্রাতিরিক্ত, ওদিকে কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। তবু তার সরল নির্বুদ্ধিতার জন্যেই সবাই তাকে ভালোবাসত। তাই বেকার হতে হয়নি তাকে কোনোদিন। গৌরাঙ্গ নিজেকে কবির দলে সরকার (কবিয়াল) বলতে গর্ববোধ করে। কোন কোন বিখ্যাত কবির দলে সে শাকরেদি করেছে তার ইতিহাসও সে নির্ভুল বলে দিতে পারে। আমরা অবশ্য জানতাম, কবি অক্ষয় সরকারের দলে থেকে ফুটফরমাশ খেটেছিল ও মাসখানেক, ব্যস, ওই পর্যন্তই তার শাকরেদি!
অমৃত হালে বিভূতি বায়েনের সাকরেদ হয়েছে। আমাদের পরামর্শমতো সে খোলে চাঁটি মারতেই গৌরাঙ্গ শুরু করে,
রামগুণাগুণ বাদ্য বাজে
গোবর্ধনের বাড়ি হে,
(আমরা দোহাররা : রামগুণাগুণ বাদ্য বাজে…)
গোবর্ধনে অম্বল খায়
হাপপুর হুপপুর হে।
মুহূর্তে দারুণ হাসির রোল পড়ে যায় ‘অম্বল’ খাওয়ার দাপটে!
আশ্বিন মাসের শেষ। দুপুরে বাড়ির বৈঠকখানার সামনে একটা বড়ো আমগাছতলায় মাদুর পেতে বসে একদিন গল্প করছিলাম আমরা জনকয়েক মিলে। এমনি সময় চন্ডীপুর (নোয়াখালি) থেকে হরেনকাকা এমন একটা সংবাদ এনে হাজির করলেন যা দুঃস্বপ্নেরও অতীত বলে বোধ হল। তিনি জানালেন, ওই অঞ্চলে দলে দলে ক্ষিপ্ত মুসলমান কয়েকটি বাড়িতে হানা দিয়ে সমস্ত ঘর অগ্নিদগ্ধ করেছে, লুণ্ঠন করেছে জিনিসপত্র, গোরুবাছুর পর্যন্ত। দুটি রোমহর্ষক হত্যাকান্ডের সংবাদও দিলেন তিনি, আর বললেন সর্বত্র এই আগুন ছড়াবার জন্যে সভাসমিতিতে প্রচারও চলছে। চব্বিশ ঘণ্টা পার হতে-না-হতেই খবর পেলাম পাশের গ্রামে অগ্নিকান্ড আর লুঠতরাজের। বেলাবেলি মেয়েদের, বুড়োদের আর শিশুদের সরিয়ে দেওয়া হল নিরাপদ স্থানে–শহরের আইন-শৃঙ্খলার মধ্যে। রাত্রিশেষে দশসহস্রাধিক মানুষের গ্রামকে শ্মশানপুরীর নিস্তব্ধতার মধ্যে নিঃশেষে শূন্য করে দিয়ে আমরা তরুণরাও জন্মভূমি, জন্মগ্রাম থেকে বিদায় নিলাম। শত শতাব্দীর ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল যে ইতিহাস, বর্বরতার হিংস্র অভিযান তাকে চুরমার করে দিল নিমেষে। ইতিহাসের এই ছিন্নসূত্র আবার কোনোদিন জোড়া লাগবে কি না কে জানে!
.
কালীকচ্ছ
গ্রাম-প্রাণ আমাদের বাংলাদেশ। অসংখ্য গ্রাম পূর্ব বাংলায়। আমরা ছেড়ে এসেছি সেসব গ্রাম। সেসব ছেড়ে-আসা গ্রামের মধ্যে কালীকচ্ছ একটি নাম–সে অন্যতমা, সে অনন্যা সে আমার গ্রাম-জননী। পূর্ববাংলার আর সব গ্রামের মতোই জল-বাতাস ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে আমার কালীকচ্ছ মহিমাময়ী। আর সবাইয়ের মতো আমারও দেহ-মনে শিহরন জাগে বহুস্মৃতি-বিজড়িত সেই জন্মগ্রামের কথা ভাবতে। মায়ের মতো করে সেই গ্রামই যে আমায় শিখিয়েছিল সংগ্রামময় এই পৃথিবীতে সংগ্রামী হয়ে বেঁচে থাকতে। আজ তাই তার অভাব মনকে পীড়িত করে, করে তোলে বিষাদ-ভারাক্রান্ত। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে একটি বড়ো কর্মকেন্দ্র ছিল কালীকচ্ছ। মুক্তিযুদ্ধের সেই ইতিহাসে কালীকচ্ছের অবদান বড়ো কম নয়। কিন্তু ভবিষ্যৎ ভারত ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায় সংযোজনায় সাময়িকভাবে হলেও সে আজ বঞ্চিত।
আজ থেকে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার কথা। সেই ছোটোবেলার কত স্মৃতিই না আজ হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে। আমাদের বাড়িকে বলা হত রামপ্রসাদের রামের পুরী। সাতমহল বাড়ি। তাতে ছিল জঙ্গলাকীর্ণ একটা পুরোনো মন্দির। শেয়াল শিকার করতে গিয়ে একদিন একটা কুকুর নিয়ে ঢুকে পড়েছিলাম সেই মন্দিরে। কিন্তু শেয়াল ধরা পড়েনি সেখানে। তাহলেও সেই মন্দিরে পাওয়া গেল একটি সুরক্ষিত বাক্স। খুব খুশি মনেই সেই বাক্স নিয়ে আমি ফিরে এলাম। প্রাণের ভয়ে যে মন্দিরের ধারে কাছেও যায় না কেউ সেখানে যাওয়ার কথা বাড়িতে খুলে বলাও তো মুশকিল। ও মন্দির নাকি ছিন্নমস্তার। কোনো এক সন্ধ্যায় ওই মন্দির থেকে এক ছিন্নমস্তা মূর্তিকে বার হয়ে যেতে দেখে আমাদেরই এক প্রপিতামহী নাকি চিরতরে জ্ঞান হারিয়েছিলেন। সেই থেকেই মানববর্জিত এই মন্দিরে অপদেবতার ভয়ে কেউ প্রবেশ করতে সাহস পায় না। সেই মন্দিরে বাক্সটি দেখে ভাবলাম হয়তো ওই দেবতারই ধনরত্ন রাখা আছে তাতে। সাগ্রহে বাড়ি নিয়ে এলাম। বাক্সটি খুলেই বাবা কীরকম গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং এ নিয়ে বেশি হইচই করতে বারণ করে দিলেন।
বাক্সটিতে যা জিনিসপত্র ছিল তা নিয়ে দেখানো হল স্বগৃহে অন্তরিন প্রমথনাথ নন্দীকে। তিনি বললেন, ওগুলো তাজা কার্তুজ, গ্রামের বিপ্লবীদের সম্পত্তি। আমার বড়ো ভাই এনে ওইখানে রেখেছিলেন।
তখন প্রমথবাবু ও অন্যান্য কয়েকজন যুবকের গতিবিধির ওপর লক্ষ রাখবার জন্যে গ্রামে গুপ্তচর ঘোরাফেরা করত। পুলিশ একবার খোঁজ পেলে হাজতে যেতে হবে সকলকেই। তাই বাক্সটি ফেলে দেওয়া হল পচা-ডোবার মধ্যে।
বিপ্লব আন্দোলনে আমাদের গ্রামের যুবকরা সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এসেছে প্রথম যুগ থেকেই। শ্রীঅরবিন্দ আমাদের গ্রামে পদার্পণ করেছিলেন ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে। পল্লি-মানুষের মনে বিপ্লব-বহ্নির ছোঁয়া লাগানো ছিল উদ্দেশ্য। বিপিনচন্দ্র পালও দু-বার আমাদের গ্রামে গিয়েছিলেন–কয়েকটি সভায় বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। আমাদের গ্রামেই জন্মেছিলেন মানিকতলা বোমা মামলার বিপ্লবী বীর উল্লাসকর দত্ত। ওই মামলা তখনও চলছে। ধরা পড়লেন আমাদের অশোক নন্দী। মামলায় জড়াবার আগেই মৃত্যু তাঁকে সরিয়ে নিলে। পরবর্তীকালে কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার ব্যাপারেও আমাদের গ্রামের বহু যুবক-যুবতি ধৃত ও অন্তরিন হয়েছিল। এক পুলিশের চরকে গুলি করা হয় আমাদের গ্রামে। সে ছিল মুসলমান। গুলি করেছিল আমাদের গ্রামেরই বিরাজ দেব। এ মামলায় ও আর একটি মামলায় তার জেল হয়েছিল মোট ৪৫ বৎসরের। মুসলমান গুপ্তচরকে মারার জন্যে সেদিন মুসলমান বন্ধুরাই সাহায্য করেছিল হিন্দুদের।
গ্রামের সভা-সমিতি ও আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল মহেন্দ্র নন্দীর বাড়ি। মহেন্দ্র নন্দী ছিলেন অশোক নন্দীর পিতা ও উল্লাসকর দত্তের মামা। মহেন্দ্রবাবুকে মহাপুরুষ বলেই জানতাম। তিনি হোমিয়োপ্যাথিক চিকিৎসা করতেন। তাঁর ওষুধ খেয়ে সুস্থ হয়নি, এরকম বড়ড়া একটা শোনা যায়নি। তাঁর হাতের পরশ পেলেও নাকি রোগী সুস্থ হয়ে যেত। অনেক দূর দেশ থেকে দুরারোগ্য সব ব্যাধি নিয়ে বহু লোক আসত। কলকাতা থেকেও অনেকে ডেকে নিয়ে যেত তাঁকে। বিখ্যাত সেতারি আলাউদ্দিন খাঁ ও তাঁর বড় ভাই আয়েতালি খাঁ ছিলেন মহেন্দ্রবাবুর শিষ্য।
মহেন্দ্রবাবু শুধু ডাক্তার ও স্বদেশি আন্দোলনের নেতাই ছিলেন না, স্বদেশি জিনিস প্রস্তুতের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অন্যতম অগ্রপথিক। এক ধরনের দেশলাইয়ের কল আবিষ্কারের কৃতিত্ব তাঁর। ঝিনুক এবং নারকেলের মালার বোতাম তৈরির কলও আবিষ্কার করেছিলেন তিনি। বাড়িতে তাঁর বিরাট কারখানায় দেশলাই, বোতাম ও তাঁতের কাপড় তৈরি হত। বহু বাঙালি তাঁর আবিষ্কৃত দেশলাইয়ের কল নিয়ে ব্যাবসা শুরু করেছিল।
মহেন্দ্রবাবু ছিলেন ব্রাহ্ম। মহেন্দ্রবাবুর বাবা আনন্দ নন্দী, কৈলাস নন্দী এবং আরও কয়েকজন একসঙ্গে ঢাকায় কেশবচন্দ্র সেনের কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছিলেন। দীক্ষাগ্রহণের পর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এসে বহুদিন আনন্দ নন্দীর বাড়িতে বাস করেছিলেন। আনন্দ নন্দী ছিলেন সিদ্ধপুরুষ। তাঁর সম্বন্ধে অনেক কাহিনি এখনও কালীকচ্ছের ঘরে ঘরে প্রচলিত আছে।
এই সেদিন আমাদের মাস্টারমশাই বৃদ্ধ নিকুঞ্জবিহারী দত্ত বললেন যে, আনন্দ নন্দী সম্বন্ধে নানা কথা শুনে তাঁরা তিন বন্ধু মিলে একবার তাঁর কাছে গেলেন। উদ্দেশ্য, পরীক্ষায় পাশ করবেন কি না তাই জানা। তিনজনই তখন আই.এ. পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরি হচ্ছেন। তাঁরা প্রশ্ন করবার আগেই আনন্দ নন্দী বললেন, ‘তোমরা যা জানতে এসেছ তা আমি একটু পরে বলব।’ বলে তিনি ধ্যানে বসলেন। ধ্যান শেষ হলে বললেন, তিনজনের মধ্যে নিকুঞ্জবাবু পাশ করবেন, একজন ফেল করবেন, তৃতীয় জন পরীক্ষাই দিতে পারবেন না। এই তিনটি ভবিষ্যদ্বাণীই ফলে গিয়েছিল।
মৃত্যুশয্যায় আনন্দ নন্দীকে তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তো চললে, আমার কী হবে? আনন্দ নন্দী জবাব দিলেন, তিন দিনের মধ্যে তুমিও আমার কাছে আসছ। মৃত্যুর পর আনন্দ নন্দীকে সমাধিস্থ করতে দিলেন না তাঁর স্ত্রী। বললেন, তিন দিন পর যেন তাঁদের উভয়কে একসঙ্গে সমাধিস্থ করা হয়। নিজে বৈধব্যের বেশও পরলেন না। শান্ত মনে স্বামীর কাছে। যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলেন। তিন দিনের দিন তিনি হঠাৎ প্রাণত্যাগ করলেন। সাড়ম্বরে তাঁদের উভয়কে সমাধিস্থ করা হল। দয়াময়ের নাম প্রচারের জন্যে সেই সমাধির ওপর মহেন্দ্রবাবু একটি মন্দির স্থাপন করেছিলেন। সেই মন্দিরে নিয়মিত উপাসনা হত সকালে-সন্ধ্যায়। কাঙালিভোজন হত প্রত্যহ।
ওই মন্দিরটি ছাড়া কালীকচ্ছে আরও একটি ব্রাহ্ম মন্দির ছিল। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্যারীনাথ নন্দী। এত অধিক সংখ্যক ব্রাহ্ম হয়তো কাছাকাছি অন্য কোনো গ্রামে ছিল না। আনন্দ নন্দীর পিতা রামদুলাল নন্দী ছিলেন দেওয়ান। তাঁর রচিত অনেক গান একসময় মুখে মুখে ফিরত। রামদুলাল নন্দী নিজের জন্যে এক বিরাট পাকাবাড়ি তৈরি করলেন। তাতে কোঠাই ছিল কুড়িটি। দুই পাশে দুই পুকুর। তাতে বাঁধানো ঘাট আর সামনে বিরাট নাটমন্দির। বাড়ি তৈরি সম্পূর্ণ হবার পরে তাঁর গুরুদেব এলেন বাড়ি দেখতে। বাড়ি দেখেই তিনি মুগ্ধ হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন এবং তা শুনে রামদুলাল গুরুদেবকে বাড়িটি দান করে দিলেন।
ত্রিপুরা জেলার সবচেয়ে বড়ড়া, সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু গ্রাম কালীকচ্ছ। চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যতরি ডুবেছিল যে কালীদহে সেই কালীদহের পলিমাটিতে গড়া এই মনোরম গ্রাম। অনেক খ্যাতনামা ব্যক্তির জন্মভূমি এই কালীকচ্ছ। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট রমেশচন্দ্র দত্ত, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তারিণী নন্দী, সুরেশচন্দ্র সিংহ, প্রকাশচন্দ্র সিংহ, এস. ডি. ও. হেমেন্দ্রনাথ নন্দী, কৃষি কলেজের অধ্যক্ষ ও বহু গ্রন্থের রচয়িতা দ্বিজদাস দত্ত, মেজর জেনারেল সত্যব্রত সিংহরায়, ব্যাঙ্ক ব্যাবসায়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ নরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত এই গ্রামের সন্তান। ত্রিপুরা জেলা থেকে মেয়েদের মধ্যে প্রথম বি.এ. পাশ করেছিলেন মৃণালবালা নন্দী। তাঁরও জন্ম কালীকচ্ছে। কুমিল্লা লেবার হাউসের প্রতিষ্ঠাতা পি. চক্রবর্তীও ছিলেন এই গ্রামেরই অধিবাসী।
কালীকচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাব ছিল না। এর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল রসিক নন্দীর পাঠশালা। এই পাঠশালায় যার হাতেখড়ি হয়েছে সে যে জীবনে কখনো অঙ্কে ফেল করবে না, এ ধারাণা ছিল প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। আরও একটি বিষয় ছিল একরূপ নিশ্চিত। অভিভাবকরা জানতেন যে, পড়ায় যে-ছাত্রের গাফিলতি হবে, রসিক নন্দীর বেতের দাগ কেটে বসে যাবে তার পিঠের চামড়ায়। সংস্কৃতে উচ্চ-উপাধিধারী ছিলেন সুরেন্দ্র তর্কতীর্থ, নৃপেন্দ্র তর্কতীর্থ প্রমুখ পন্ডিতরা। এঁদের বাড়িতে টোল ছিল। বিভিন্ন জেলা থেকে ছাত্ররা এসে টোলে পড়াশোনা করত। উদাত্ত কণ্ঠের সংস্কৃত পাঠের সুরে মুখরিত হয়ে থাকত কালীকচ্ছের প্রভাতী আর সান্ধ্য আকাশ। আজ সে গ্রামকে ছেড়ে দিয়ে আসতে হল পাকিস্তানের কবলে। সেই বৃহৎ গ্রামের মধ্যে একটি বাড়িও ছিল না মুসলমানের। আশপাশে অবশ্য অনেক গ্রামই ছিল মুসলমানপ্রধান, তবে ভয়-ভাবনা আমাদের কোনোদিনই ছিল না তার জন্যে।
তারপর আমোদ-আহ্লাদের কথা। সে-কথা ভাবলেও আজ মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। মনে পড়ে উপেন্দ্রবাবুর যাত্রার দলের ‘বিজয় বসন্ত’ পালার কথা। সরাইল হাইস্কুলের কেরানি ছিলেন উপেন্দ্রবাবু। অবসর সময়ে যাত্রার দলের মহড়া হত তাঁর বাড়িতে। তাঁরই প্রচেষ্টায় যাত্রার দলটি গড়ে উঠেছিল। দলটির খ্যাতিও ছড়িয়ে পড়েছিল চারিদিকে। খালি মাঠে শামিয়ানা খাঁটিয়ে শীতের রাতে আটটা-ন-টার সময় যাত্রা আরম্ভ হত। এখনও চোখে ভাসে কয়েকটি দৃশ্য।…বসন্তকে মারবার হুকুম দিলেন রাজা। জহ্লাদ এসে উপস্থিত হল। সে যখন সাড়ে ছ-ফুট লম্বা দশাসই চেহারা নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়াত, ভয়ে আমাদের শিরদাঁড়া দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যেত, লোমগুলো হয়ে উঠত খাড়া। আমাদের শিশুকালের সেই রোমাঞ্চকর স্মৃতি আজও একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। এই যাত্রার দলটিকে শ্রীহট্ট ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা টাকা দিয়ে নিয়ে যেত।
একবার দলটি মেঘনা নদীর বন্দর ভৈরব বাজারে গেল ‘বিজয় বসন্ত’ পালা অভিনয় কররার জন্যে। শীতের রাত। পালা এত জমে গেল যে, বিজয় ভুলে গেল সে অভিনয় করছে। বসন্তের বুকে সজোরে ছুরি বসিয়ে দিল। শেষপর্যন্ত ডাক্তারই ডাকতে হল রক্ত বন্ধ করার জন্যে। এই যাত্রা শোনার জন্যে আমরা সন্ধে না হতেই বাড়িতে কান্নাকাটি করে বাবা মার মত আদায় করে আসরে এসে বসতাম। একেবারে সামনের আসনে বসতে না পারলে কিছুতেই মন সন্তুষ্ট হত না। কিন্তু আমাদের চেয়েও সেয়ানা লোক ছিল। তারা এসে হঠাৎ ‘সাপ সাপ’ বলে চেঁচিয়ে উঠত। আমরা তখন সাপের ভয়ে পড়ি-কি-মরি করে দে-ছুট। তারা সেই সুযোগে এগিয়ে এসে সামনের আসনগুলি দখল করত। কখনো কখনো এ নিয়ে মারামারি পর্যন্ত লেগে যেত। সেদিন নিজের জায়গাটি পুনরুদ্ধার করতে পারলে স্বর্গরাজ্য পুনরুদ্ধারের আনন্দ পাওয়া যেত।
এর ওপর ছিল পাড়ায় পাড়ায় ফুটবল, দাঁড়িয়াবান্ধা, গুটিদাঁড়া খেলার প্রতিযোগিতা। তেঁতুল কাঠের সার দিয়ে পিংপং-এর বলের মতো আকারের কালো কুচকুচে বল তৈরি হত। সেই বলটিকে মারবার জন্যে কাঁচা বাঁশ দিয়ে তৈরি হত দাঁড়া অর্থাৎ ব্যাট। ক্রিকেট খেলার সঙ্গে এর তুলনা চলে। রজনী ডাক্তার প্রচন্ড জোরে বল পিটাতেন, ক্রিকেটের ওভার বাউণ্ডারির চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় হত তা।
গ্রামেই ছিল বাজার। গ্রামেই ছিল পোস্ট-অফিস। তা ছাড়া রক্ষাকালী, শ্মশানকালীর বাড়ি। রক্ষাকালীর বাড়ির পুজোয় মহিষ-বলির পর দড়ি কে নেবে তা নিয়ে লেগে যেত পাড়ায় পাড়ায় প্রতিযোগিতা। যে পাড়া দড়ি পাবে সে-ই জয়ী সাব্যস্ত হবে। দত্তবংশের দাতা গোপীনাথ দত্তের নাম না করলে কালীকচ্ছের কথা বলা শেষ হয় না। অবশ্য শেষ কোনো দিনই হবে না। জন্মভূমির কাহিনি কবে আর শেষ হয়? সে যাক– গোপীনাথ দত্তের কথাই বলি। গোপীনাথ পুকুর থেকে স্নান করে ফিরছেন। হঠাৎ এক ভিখারি এসে সামনে দাঁড়াল। গোপীনাথের কাছ থেকে সে কিছু চায়। দেবার মতো কিছুই ছিল না গোপীনাথের। কিছুক্ষণ ভাবলেন গোপীনাথ। তারপর গামছাটি পরে কাপড়টি দিয়ে দিলেন ভিখারিকে।
দিনাজপুর – ফুলবাড়ি রাজারামপুর
বাংলাদেশের উত্তর ভূখন্ডের গ্রাম ফুলবাড়ি। রাঙামাটির পথ এখান থেকে শুরু হয়ে দিগন্তে হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে। পদ্মা-মেঘনার দোলন-লাগা ছায়া-সুনিবিড় পূর্ব-বাংলার গ্রামের তুলনায় দিনাজপুরের এই পল্লিশ্রী একটু বিশেষ বৈচিত্রময়। এখানে অরণ্যের অনাহত সারল্য উদ্দাম হয়ে উঠেছে গ্রামান্তের আদিবাসী নর-নারীর মাদল-দোলানো নৃত্যের তালে তালে। পান্ডববর্জিত পূর্ব-বাংলা থেকে এই বরেন্দ্রভূমি এদিক দিয়ে নিজের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছে। কলকাতার কর্মমুখর জনস্রোতে আজ নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি। যে গ্রামের বুকে পিতৃ পিতামহের স্মৃতি প্রতিটি বৃক্ষ-লতায় পথের ধূলিকণায় মিশে আছে তার সঙ্গে আজ দুস্তর ব্যবধান। ফুলবাড়ি আর আমার নিজের বাড়ি নয়, সেখানে আমি অনাহূত। এ নির্মম সত্য বিশ্বাস করতে মন চায় না, অবিশ্বাস যে করব মনের সে জোরই বা কই?
৩সে. গ্রাম যে কী জিনিস, আজ তাকে হারিয়ে মর্মে মর্মে তা অনুভব করতে পারছি।
দুর্গোৎসবের সময় সাড়া পড়ে যেত পাড়ায় পাড়ায়। সোনার আঁচল বিছিয়ে শরতের রানি আসছেন। তাঁর আগমনি-সুরে সুরেলা হয়ে উঠেছে ফুলবাড়ির আকাশ, বাতাস, প্রকৃতি। এ তো শুধু পুজো নয়, এ যে আমাদের জাতীয় উৎসব! এ উৎসবকে কেন্দ্র করে মিলিত হতাম সমস্ত গ্রামবাসী। শ্রেণি সম্প্রদায়ের প্রশ্ন সেখানে নেই, আর্থিক সংগতির প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সে উৎসবে সকলে মিলিত হয়ে আনন্দ করেছি, সে মিলনের মধ্য দিয়ে গ্রামের সহজ সরল আত্মীয়তার মধুর স্পর্শ করে ধন্য হয়েছি।
সবচেয়ে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে বিজয়াদশমীর দিনটি। প্রিয়জনের বিচ্ছেদ বেদনায় মতোই সেদিনটি অশ্রু-টলমল। পুণ্যতোয়া করতোয়ার তীরে বিসর্জনের বাজনা বাজছে। সে উৎসব উপলক্ষ্যে সমবেত হয়েছে এসে সাঁওতাল-আদিবাসী ছেলে-মেয়ে স্ত্রী-পুরুষের সব দল। তাদের চিকন কালো যৌবনপুষ্ট দেহল-সৌষ্ঠব কেশপাশে কৃষ্ণচূড়ার অপূর্ব বিন্যাস সমারোহ। মাদলের তালে তালে শুরু হত তাদের লোকনৃত্য। কোথায় সেদিন, কোথায় সেই অরণ্যলালিত মানুষের নৃত্যছন্দের হিল্লোল! আজ সে সব স্বপ্ন বলেই মনে হয়।
উৎসবের দেশ বাংলার গ্রামে এসেছে দোলপূর্ণিমায় হোলিখেলার দিন। বসন্তে রং লেগেছে ফুলবাড়ির আকাশে। দিকে দিকে গান শুরু হয়েছে ‘দখিন দুয়ার খোলা। সেই ফাল্গুনের উজ্জ্বল রোদে আমরা দল বেঁধে বেরিয়ে পড়তাম গ্রামের পথে। আমাদেরই কাউকে হোলির রাজা বানিয়ে দিতাম শিবের মতো সাজিয়ে। তার পেছন পেছন সকলে হোলির উৎসবের হই হল্লায় গ্রামের পথঘাট মাতিয়ে তুলতাম। ছড়িয়ে দেওয়ার, ভরিয়ে দেওয়ার সে আনন্দে হোলির দিনগুলো আজও মনকে দোলা দিয়ে যায়।
বারোয়ারিতলায় এক-একদিন বসত কীর্তনের আসর। মাথুর পালা শোনবার আকর্ষণে হাজার লোকের ভিড়। ভিনগাঁ থেকে এসেছে নামকরা কীর্তনীয়া। প্রতিবেশী মুসলমানরাও বাদ পড়েনি সে গানের আসরের আমন্ত্রণ থেকে। মাথুরের অশ্রুসজল কীর্তনের সুরে মুগ্ধ হয়ে কেউ-বা হয়তো মেডেল পুরস্কার দিতেন কীর্তনীয়াকে। মুসলমান শ্রোতারাও অনেক সময় দিয়েছেন উপহার। সেদিন তো ধর্মের কোনো বালাই ছিল না। স্কুলে মুসলমানদের পর্ব ‘মিলাদ শরিফ’ হয়েছে, হিন্দু ছাত্ররাও তাতে অংশ গ্রহণ করেছে বিনা দ্বিধায়। সেদিন তো কোনো জাতির প্রশ্ন, ধর্মের প্রশ্ন পরস্পরের এই প্রীতির সম্পর্ককে এমন বিষাক্ত করে তোলেনি। আজ কেন এই অন্ধ উন্মত্ততা?
আজও মনে পড়ে আমাদের গ্রামের সর্বজনপ্রিয় আবদুল রউফ সাহেবের মৃত্যুর দিনটি। তাঁর মৃত্যুর সংবাদে সবার চোখে সেদিন জল এসেছিল। হিন্দু-মুসলমান সকলে সেদিন যোগ দিয়েছিল রউফ সাহেবের শবযাত্রায়। তাঁর সমাধি হিন্দু-মুসলমান অনুরাগীর শোকাশ্রুতে সেদিন স্নাত হয়ে গিয়েছিল। সেদিনের স্মৃতি আজও তো মন থেকে মুছে যায়নি!
দরিদ্র পল্লি-বাংলা। ফুলবাড়িও তেমনই দরিদ্র পল্লি। গ্রামবাসী অনেকেরই আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না। তবু তাদের মনে সুখ ছিল। আর ছিল প্রতিবেশীর প্রতি অসীম মমত্ববোধ। এই আত্মীয়তার স্পর্শেই গ্রামবাসী মানুষের জীবন সেদিন মধুময় হয়ে উঠেছিল।
গ্রাম থেকে উৎখাত হয়ে নগরে এসে আজ আস্তানা গড়েছি। এ মহানগরীর সঙ্গে শুধু দেনা-পাওনার সম্পর্ক, প্রাণের কোনো যোগ নেই এখানে। গ্রামের মাটিতে সবুজ তৃণলতা থেকে শুরু করে সব কিছুর সঙ্গেই যেন একটা মধুর প্রীতির সম্পর্ক পাতানো ছিল। দেশবিভাগের ফলে সেই মাটির মাকে হারিয়েছি। ছিন্নমূলের ভূমিকায় আজ আমরা নিজেদের হারিয়ে ফেলেছি অজানার ঘূর্ণাবর্তে। আমরা ফিরে পেতে চাই সেই মাটিকে। ফিরে যেতে চাই রাঙামাটির দেশে, সেই উত্তর বাংলার নিভৃত পল্লি-পরিবেশে।
ফুলবাড়ির রূপ আজ কেমন দাঁড়িয়েছে জানি না।
আধ-পাগলা সেই বিলাসী বৈরাগী আর হয়তো একতারা বাজিয়ে গান ধরে না–’চল সজনি যাই গো নদিয়ায়। বাউলের আখড়ায় সন্ধের দিকে আর আড্ডাও হয়তো বসে না। কিন্তু আমাদের পাশের বাড়ির ডাক্তারবাবুর বাগানের গন্ধরাজ গাছটির ফুলের গন্ধ নিশ্চয়ই অকৃপণ দাক্ষিণ্যে পূর্ণ করে দেয় অঙ্গনতল। রজনিগন্ধার ঝাড় থেকে অফুরান মনমাতানো সৌরভ এখনও হয়তো ফুলবাড়ির পথঘাটে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু আমাদের বাসুদেবের ভাঙা দেউলে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাবার মতো কেউ আর বোধ হয় সেখানে নেই। ফুলবাড়ির নিষ্প্রদীপ দেউলে মানুষের ভগবান কী তপস্যায় মগ্ন কে জানে?
.
রাজারামপুর
কোথা থেকে যেন কী হয়ে গেল। যে ছিল একান্ত আপন সেই হয়ে গেল পর। স্বদেশকে স্বাধীন করবার মূল্য দিতে হল এইভাবে? মূল্য হিসেবে দিতে হল গ্রামজননীকে। আমাদের স্বাধীনতা তাই এল মহাবিচ্ছেদের কান্নায় ভিজে হয়ে!
আমার গ্রামের নাম রাজারামপুর। দিনাজপুরের অনেকগুলো গ্রামের একটি। রাজারামপুর ভাটপাড়ায় এসে পৌঁছোলে মনে হয় বাংলার সাধারণ গ্রাম থেকে এর চেহারা যেন একটু পৃথক। তবে রংপুর, রাজসাহী, নাটোর–এসব অঞ্চলের গ্রামের সঙ্গে মিল রয়েছে অনেকটাই। চারিদিকে শটীর জঙ্গল আর আটিশ্বরের ঝোঁপ। আম-জাম-কাঁঠালের বন মাঝে মাঝে এতই নিবিড় হয়ে উঠেছে যে হঠাৎ ঠাহর করাই শক্ত সেই বনের মধ্যে কোথায় কার খড়ের চালা মাথা উঁচু করে আছে।
দিনাজপুরের বালুবাড়ি শহরের অনেকটা কাছে, তাই তার গ্রাম্য চোহারা কিছুটা বদলেছে। কিন্তু তারই বুক চিরে মহারাজ হাই স্কুলের পাশ দিয়ে যে মেঠো পথ বনজঙ্গল ভেদ করে রাজারামপুর-ভাটপাড়ায় গিয়ে পৌঁছেছে, সে পথ দিয়ে দিনের বেলায় একা হাঁটতে কেমন যেন ভয় করে। কিছুদূর পথ চলার পরই ধুলো হাঁটু অবধি উঠে আসবে। গোরুর গাড়ির মন্থর গতি দেখে বেশ বোঝা যায় যে চাকা ধুলোর ভেতর দিয়ে কোনোরকমে এগিয়ে চলেছে। তবু ও-পথটার এমনই একটা আকর্ষণ আছে, সেপথে না গেলে তা বোঝা সহজ নয়। বালুবাড়ির সীমানা পার হওয়ার পরই দেখা যাবে বাঁ-দিকে কুমোরদের পল্লি। মাটির বাসন-কোসন ছাড়া এরা খাপড়াও তৈরি করে থাকে–শহরের লোকের খাপড়ার চাহিদা রোজই বাড়ছে।
তারপরই জলা-জঙ্গল পার হয়ে আম-কাঁঠাল গাছের সারি। পথের দু-ধার থেকে তারা যেন ইশারায় ডেকে নিয়ে যায়। তারপরেই রাজারামপুর ভাটপাড়া।
রাজারামপুর-ভাটপাড়া–এই দুই গ্রামের নাম পৃথক হলেও প্রকৃতপক্ষে ও-এলাকাটাকে একটা গ্রাম ছাড়া ভাবা যায় না। দুই গ্রামের মধ্যে শুধু ছেলেদের বল খেলার একটি বিস্তীর্ণ মাঠ। এই মাঠেরই একধারে রাজারামপুর আর একদিকে ভাটপাড়া।
পরাধীনতার যুগে এই অরণ্যঘেরা এলাকায় মাত্র কয়েক ঘর মানুষের বসতির মধ্যে থেকে ‘হিলি ডাকাতি’র প্রেরণা কীভাবে লোকে পেয়েছিল তার কাহিনি চিত্তাকর্ষক। এই সব এলাকায় ঘুরে বেড়িয়েছি–কিন্তু হিলি ডাকাতির মামলার কথা সাধারণত কেউ বলতে চাইত না। শুনতাম, হৃষি এবার জেল থেকে বার হবে। কত অল্প বয়সে পুলিশ ওকে ধরে নিয়ে গেছে। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। বালুবাড়ি, ক্ষেত্রিপাড়া, কালীতলা, বড়োবন্দর-এ সব জায়গার কে na জানে পরমধার্মিক রমেশ ভট্টাচার্যকে। তাঁরই ছেলে হৃষি। লেখাপড়ায় আর আদবকায়দায় তার মতো ছেলে মেলা ভার। রমেশবাবু বন্দরে নিজের বাড়ি করেছিলেন। কিন্তু তাঁর শরিক দেবেশ ভট্টাচার্য ভাটপাড়াতেই থাকতেন। পৈতৃক সম্পত্তি অগাধ। দেবেশবাবু ছিলেন শৌখিন ও আমুদে প্রকৃতির লোক। হঠাৎ একদিন হৃষি ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে কয়েকজন কিশোর এল বড়োবন্দর বালুবাড়ি থেকে ভাটপাড়ায়। এমন তারা প্রায়ই আসে। সকলের গায়েই আলোয়ান। দেবেশবাবু বাড়ি নেই।
তখন বাড়িতে নতুন নতুন কয়েকটা আগ্নেয়াস্ত্র এসেছে। হৃষির দলবলের আগ্রহে দেবেশবাবুর স্ত্রী একে একে ওদের সেগুলি সব দেখালেন। তারপর চামড়ার ‘কেসে’ বন্ধ করে তুলে রেখে দিলেন। খাওয়া-দাওয়া সেরে ছেলেরা হাসিমুখে প্রণম্যদের প্রণাম করে বেরিয়ে গেল।
তারপরই ওরা নিরুদ্দেশ। কিছুদিনের মধ্যে হিলি ডাকাতির মামলার বিশ্বরূপ প্রকাশ পেল। দেখা গেল হৃষিও অভিযুক্ত। একনম্বর আসামি ইংরেজের আদালতে। খবর শুনে ধর্মপ্রাণ রমেশবাবু মর্মাহত। কিন্তু হৃষির প্রাণভিক্ষার আপিলও তিনি নাকি করতে চাননি।
পরে দেখা গেল দেবেশ ভট্টাচার্যের বাড়িতে রিভলবারের চামড়ার কেসগুলো ঠিকই আছে, তবে তারমধ্যে থেকে আসল জিনিস উধাও হয়েছে।
আর ওই-উপজাতি পোলিয়ারা। ওদের প্রভাব বাসিন্দাদের ওপর প্রচুর। ওদের স্ত্রী-পুরুষ শটী জঙ্গলে কাজ করে। হলুদের মতো শেকড় তুলে চালনি-টিনে ঘষে ঘষে কাত বার করে। তারপর সে কাত ধুয়ে ধুয়ে, শুকিয়ে নিয়ে তৈরি করে শটী। ওদের সঙ্গে ওদের ভাষাতেই কথা কইতে হয়–’খাবা নাহে’, ‘এলাই বাহে’ ইত্যাদি। পিঠে নবজাত শিশুকে বেঁধে নিয়ে মাঠের কাজ করছে, মুড়ি বিক্রি করছে তাদের রমণীরা। এদের ভাষার প্রভাব অল্পবিস্তর পড়েছে সকলের ওপরই। অবশ্য মুখের ভাষাতেই এই প্রভাব সীমাবদ্ধ–লেখার ভাষায় নয়।
রাজারামপুর-ভাটপাড়া জঙ্গল আর পানাপুকুরে ভরা। তবু বন-জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে কত যে দেব-দেবীর মূর্তি আছে তার বোধ করি সীমা-সংখ্যা নেই। রাজারামপুরের ভদ্রকালী অতিজাগ্রত বলে খ্যাত। তেমনই আবার ভাটপাড়ার শ্মশানবাসিনীর মন্দির। শ্মশানবাসিনীর মন্দির দূর থেকে দেখলেই ভয় লাগে। বনজঙ্গল-ঘেরা এই জীর্ণ মন্দির। আরও কত জায়গায় ছড়িয়ে আছে শিবলিঙ্গ আর কালীমূর্তি।
আষাঢ় থেকে শীতের আগে অবধি গ্রামে ম্যালেরিয়ার তান্ডব। তবু পুজোর সময় দেখা যায় একাধিক দুর্গাপ্রতিমা। ঢাকের আওয়াজে মুখরিত চারিদিক। যুবকরা মাঠে মাঠে বাঁধে থিয়েটারের স্টেজ। সারারাত ধরে কোথাও হয় আলমগির, কোথাও বঙ্গে বর্গি। দেশলাইয়ের বাক্সে কুইনাইনের পিল নিয়েও থিয়েটারে মাততে দেখেছি অনেককে।
আর আছে কান্তজিউয়ের মন্দির। সে মন্দিরের কারুকার্য দেখে মনে হয় কোথায় লাগে গয়ার মন্দির! দিনাজপুর রাজপ্রাসাদে যখন কান্তজিউকে মিছিল করে নিয়ে আসা হয়–সমগ্র শহর ও গ্রামগুলো যেন জেগে ওঠে উৎসবের আনন্দে। রাজবাড়িতে দেবতার অন্নভোগ হয় না–কিন্তু এই সময় অতিথির সেবা আর অন্নদান হয়। বছরের বাকি-কয়েক মাস কান্তজিউ থাকেন কান্তনগরে। বিখ্যাত গোষ্ঠমেলা আর রাসমেলার সময় কত দূর-দূরান্তর থেকে কত ব্যাপারী আসে। মেলা চলে একমাস। কান্তজিউয়ের ভোগের পর প্রধান সেবায়েত তাঁকে চাঁদির গড়গড়ায় তামাক সেজে দেন।
এ সম্বন্ধে একটি গল্প শোনা যায়। একবার এক অতিথি দর্শনলাভের আশায় কান্তজিউয়ের মন্দিরে আসে। রাত বেশি হয়ে যাওয়ায় বাইরের বারান্দায় শুয়ে সে বিশ্রাম করতে থাকে। রাতে গড়গড়া টানার শব্দে সে তামাক খেতে ইচ্ছে করে এবং তাকে ‘একজন’ সেই চাঁদির কলকে এনে-দিয়ে যায়। পরের দিন কান্তজিউর কলকে বাইরে পড়ে থাকতে দেখে মন্দিরে গোলমাল বেধে যায়। সেই আগন্তুককে নিগ্রহ ভোগ করতে হয়। সেই থেকে নাকি কান্তজির তামাক খাওয়ার শব্দ আর শোনা যায় না।
পৌষ-সংক্রান্তি খুব ধুমধামের সঙ্গে পালিত হত। আঙিনায় আলপনা দিয়ে ঘরের দরজার মাথায় পিঠেলুর চিত্র এঁকে শোলার ফুলগুচ্ছ ধান-দূর্বার সঙ্গে ঝুলিয়ে দেওয়া হত। সব বাড়িতেই নানারকম পিঠে তৈরি হত এবং কারুর বাড়ির পিঠে ইচ্ছে হলে বিনা নিমন্ত্রণেই সে বাড়িতে গিয়ে খাওয়া যেত।
এ এলাকার লোকসংগীতের উল্লেখ না করলে বিবরণ অবশ্যই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। উত্তর-বাংলার ভাওয়াইয়া, ‘চটকা’ প্রভৃতি গান এই গ্রামেও শোনা যায়। একটি চটকা গানেরই দৃষ্টান্ত দিচ্ছি,
ডাল পাক কররে কাঁচা মরিচ দিয়া,
গুরুর কাছে নেওগা মন্তর নিরালে বসিয়া,–
ডাল পাক কর রো।
ছোটোবউ চড়ায় ডাল মাঝলা বউ ঝাড়ে,
(হারে) বড়োবউ আসিয়া কাঠি দিয়া নাড়ে।
ডাল পাক কর বরা।
(আমার) শ্বশুর করে ঘুসুর-ঘুসুর
ভাসুর করে গোসা,
(আজি) নিদয়া এল স্বামী এসে ধরল
চুলের ঘোসা,
ডাল পাক কর রো।
(আমার) শাশুড়ি আছে, ননদ আছে,
আছে ভাগনা-বউ,
এমন করে মার মারিল আইগ্যালো না কেউ,
ভাল পাক কর রো।
এমন কিছু নয়। সংসারের একটি ছোটো ছবি। রান্না, শ্বশুরের অভিযোগ, স্বামীর মারধোর, অসহায় স্ত্রীর আক্ষেপ এই তো ছবি। কিন্তু আন্তরিকতায় ভরা। গ্রামের বৈশিষ্ট্যই যে এই আন্তরিকতা। তার ছোঁয়া আমাদের বুকেও লেগেছিল। আজ সে গ্রাম স্বাধীন ভারতের দেশের বাইরে চলে গেছে। তবু তার সেই স্পর্শ আজও অম্লান।
নোয়াখালি – দরাপনগর সন্দীপ ত্রিপুরা বায়নগর চান্দিসকরা বালিয়া কালীকচ্ছ
পূর্ববঙ্গে প্রথম দুর্ভাগ্যের কালো ছায়া নেমে আসে আমাদের নোয়াখালিতে। সাম্প্রদায়িক খঙ্গাঘাতে দ্বিখন্ডিত হয়েছি আমরা, কিন্তু তবু আমরাই একদিক দিয়ে ভাগ্যবান। এই নোয়াখালির বুকের পাঁজরে পাঁজরে পড়েছিল মহাত্মার চরণচিহ্ন। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তাঁর ঐতিহাসিক পরিক্রমা সমস্ত পূর্ববাংলার বুকে একদিন এনেছিল চাঞ্চল্য। ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠার পক্ষে এই গ্রাম সফরই যথেষ্ট। শ্রীচৈতন্যের পুণ্যস্পর্শে নবদ্বীপ যেমন ধন্য, তেমনি ধন্য হয়েছে নোয়াখালি মহাত্মাজির পুণ্য পাদস্পর্শে। বৈষ্ণবযুগের জগাই-মাধাইরা কি সব নতুন করে জন্ম নিয়েছে পূর্ববাংলার পল্লিতে পল্লিতে? ইতিহাসের পশ্চাদপসরণের অর্থই হল হানাহানি, বিশ্বাসঘাতকতা, গুপ্তহত্যা, ভ্রাতৃবিরোধের কলঙ্কময় সমষ্টিফল। আমরা সে-কথা বুঝেছি অক্ষরে অক্ষরে, বুঝেছি আজ সর্বস্ব খুইয়ে। যাদের ভূমি যায় হারিয়ে তাদের ভূমিকা যে কী হতে পারে তাও ভাববার বিষয়!
এক দেশের অবাঞ্ছিত মানুষ অন্য দেশের ভারস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছি যেন আমরা, অমৃতবঞ্চিত পূর্ববাংলার অভিশপ্ত মানুষেরা আবার কবে এবং কী করে, স্বঐতিহ্যে, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে তার শুভ ইঙ্গিত বা গোপনমন্ত্র কে বলে দেবে?
মনে পড়ছে ভোর পাঁচটায় হরিনারায়ণপুর থেকে যেদিন আমাদের স্টিমার ভোঁ বাজিয়ে অজানা রাজ্যের দিকে যাত্রা করল সেদিন পূর্বাকাশের উজ্জ্বল শুকতারাটি পর্যন্ত যেন লজ্জার, শঙ্কায়, অভিমানে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। হু-হুঁ শব্দে জল কেটে নিস্পৃহ যন্ত্রদানব চলছে এগিয়ে সাত-পাঁচ কোনো কথা না চিন্তা করেই–ব্যথাতুরা জননীর বুকের ভেতর গুমরে গুমরে উঠছে আর সেই হৃদয়-নিঙড়ানো ধড়ফড়ানির ঢেউ এসে লাগছে আমারও বুকে। স্নেহময়ী মাকে শেষবারের মতো দেখে নেবার জন্যে আমি দাঁড়িয়েছিলাম ডেকে–কিন্তু অশ্রুভারে সমস্ত কিছু তখন হয়ে উঠেছে অস্পষ্ট। মায়ের রূপ গেছে হারিয়ে। ইঞ্জিনের শব্দ শুনে আমার মনে হচ্ছিল দেশজননী যেন বলছেন, ফিরে আয়–ফিরে আয়–ফিরে আয় আপন ঘরে! লক্ষ করলাম চতুর্দিকে ফিরে আসার ইঙ্গিত, আমাদের না যেতে দেবার আহ্বান।
কিন্তু আমি দুর্বল মানুষ; আমার উপায় নেই থাকবার। দোটানায় পড়ে চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে শুধু অক্ষমতার তপ্ত অশ্রু। সেদিন দেশজননীর কোল থেকে বিদায় নেবার পর থেকে যে অশ্রুবর্ষণ শুরু হয়েছে তার শেষ কোথায় জানি না। আজ এই বিশাল অনাত্মীয় পাষাণপুরীর এক কোনায় একখানি প্রায়ান্ধকার ঘরে বসে ধুকছি, মাথা পড়েছে নুয়ে, দুর্ভাবনায় চোখের পাশে কালিমার ছাপ দেখা দিয়েছে। ছাত্রজীবনের রঙিন স্বপ্নরেশগুলি আজ কঠিন বাস্তবের আঘাতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে আসার সময় তার বুকে যে উত্তাল তরঙ্গরাশির নৃত্যরূপ দেখেছিলাম তারই মধ্যে ভাসিয়ে দিয়ে এসেছি আমার সমস্ত আশা-ভরসা। উদবাস্তু স্টিমারের যাত্রী আমরা, আমাদের আশার স্বপ্ন দেখার সময় আছে? আমরা ওপারের অবাঞ্ছিত আর এপারের বোঝা হয়ে জীবন কাটাচ্ছি। সময় সময় দুঃখের আধিক্যে সজোরে মাথা ঠুকতে ইচ্ছে করে মাটিতে, কিন্তু কোথায় আমার সেই মিষ্টি দেশের মাটি?
নোয়াখালি। বাংলামায়ের সর্বকনিষ্ঠা স্নেহ-দুলালি নোয়াখালি। মহাত্মার পাদস্পর্শে ধন্যা নোয়াখালি। সারাবাংলার অণু-পরমাণু দিয়ে গড়া সমুদ্রসৈকতে দাঁড়িয়ে আমার নোয়াখালি। তারই কোলে শিশু গ্রাম আমার প্রিয় দরাপনগর’। এ গ্রামের কোনো ঐতিহাসিক পটভূমিকা আছে কি না জানি না। শুধু জানি দরাপনগর নামটি মনে পড়লেই চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ভেসে ওঠে আম-কাঁঠাল, সুপারি, নারকেলকুঞ্জ-ঘেরা একটি মনোরম দ্বীপপুঞ্জের প্রাণমাতানো ছবি। দু-পাশে ‘বারুই’-এর বরজ নিয়ে এঁকে-বেঁকে চলে যাওয়া পল্লিপথ, আশপাশে সুসজ্জিত কুঞ্জের মতো প্রতিবেশীদের বাড়িঘর, স্নেহমমতায় ভরা মন। তারই মধ্যে দু-পাশে দুটি বিরাট পুকুর নিয়ে আমাদের বাড়ি। ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্তের প্রয়োজনাতিরিক্ত সাজসরঞ্জাম নিয়ে সাজানো ঘরগুলো। পুবদিকের খানিকটা বাদ দিয়ে চারপাশ ঘেরা ছিল সুপারিকুঞ্জে।
দু-বাড়ির মাঝখানে ছোট্ট একটি ‘জুরি’। জুরিটি দুই বাড়ির অধিকারের সীমানা নির্ধারণ করলেও মানবিক গুণের সীমানা নির্ধারণ করেনি কখনো। তাদের প্রাণের মিল, মনের ছন্দ জুরির ওপর দেওয়া সুপারির পুলের অপেক্ষা করে না। পূর্বদিক রতনপুকুর। ওতে ডুব দিলে রতন পাওয়া যায় কি না জানি না, তবে তার কাকচক্ষু জল গ্রামের অধিকাংশ লোকই পানীয় জল হিসেবে ব্যবহার করত অন্য পুকুর ছেড়ে। এই রতনপুকুরের পাড় দিয়ে কচুবাড়ির দরজা দিয়ে চলে গেছে গেঁয়ো রাস্তা। কচুবাড়িতে কি শুধু কচুই হয়? শব্দ তাত্ত্বিকদের বিচার এখানে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে, এরকম বহু অসামঞ্জস্যই আছে বাংলার পল্লিতে পল্লিতে। কচুবাড়ি আমাদের কাছে পরিচিত তার ফুল বাগিচার জন্যে–অতি প্রত্যূষে উঠে ফুল চুরি করতে যেতাম কচুবাড়ি! আজ বোঝাতে পারব না সেদিনকার দু-একটা ফুল চুরির মধ্যে আমাদের শিশুমনে কী উন্মাদনা জাগত।
কচুবাড়ি থেকে রাস্তা এঁকেবেঁকে ঘেরীর বিরাট দিঘির পাড় দিয়ে চলে গেছে কাবির হাটের দিকে। দিঘির পাড় এত উঁচু হয় জানতাম না, ওপর থেকে নীচে তাকালে মাথা ঝিমঝিম করে ওঠে। তার উত্তর পাড়ের মাঝামাঝি অংশটা ভাঙা দেখে একবার কৌতূহলবশেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম বাবাকে তার কারণ। সেদিন বাবার কাছ থেকে যে উত্তর পেয়েছি তার বিস্ময় আজও কাটেনি, কিশোরমনে দাগ কেটে বসে গেছে। তিনি বলেছিলেন ওই ফাঁকটা দিয়েই নাকি একটি বিরাট সিন্দুক (যতখানি ভাঙা ততখানি মাপের) ক্রোশখানেক দূরে ‘কিল্লার দিঘিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল রাত দুপুরে। সেই বিরাট সিন্দুকে ছিল সাত রাজার সম্পদ। গ্রামবাসীরা বলে এই সিন্দুক চালাচালির ব্যাপারটি নাকি প্রায়ই নিশুতি রাত্রেই হয়ে থাকে বলে প্রবাদ আছে। বহুবার ভাঙা অংশটুকু মেরামতের চেষ্টাও হয়েছে, কিন্তু বাঁধা যায়নি কোনো-না-কোনো আশ্চর্য কারণে। শেষে ধৈর্য হারিয়ে লোকে হাল ছেড়ে দিয়েছে।
মনে পড়ছে কতদিন রাত্রে রূপকথা শোনার বায়না নিয়ে মাকে বিরক্ত করেছি, ঘুমুতে দিইনি। আজও টুকরো টুকরো খেইহারা হয়ে স্মরণপথে বড়ো হয়ে দেখা দেয় সেই তেপান্তরে ছুটে-চলা দুঃসাহসিক রাজপুত্তুর, যার ঘোড়া এখনও জোর কদমে ছুটে চলেছে মনের রাজপথে ধুলো উড়িয়ে। সেই অনাদিকালের রাজপুত্তুরের পথের সাথি হলাম আজ আমরা! আমরাও ছুটে চলেছি তেপান্তরের রুক্ষ-শুষ্ক মাঠের ওপর দিয়ে সামান্য নিরাপদ আশ্রয়ের জন্যে। জানি না এই ছুটে চলার শেষ কোথায়? ছোটোবেলায় চাঁদের ছুটে-চলা দেখে আশ্চর্য হয়েছি। এত জোরে সাদা-কালো, মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদ অমন করে ছোটে কেন? আমি যেখানে যাই চাঁদও সেখানে যায় কেন ইত্যাদি প্রশ্নে মন হয়ে উঠত ভরপুর! কতদিন চাঁদকে পেছনে ফেলে যাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছি ভেবে আজ হাসি পায়।
শিশুমনের বিস্ময় কাটিয়ে উঠে একদিন লক্ষ করলাম আমার জগৎটা হঠাৎ যেন বেড়ে গেছে অনেকখানি। আমি চষে বেড়াচ্ছি সারাগ্রামটা, গ্রামের প্রতি অণুপরমাণুর সঙ্গে আমার হয়ে গেছে একাত্মবোধ। আম, জাম, লিচু, জামরুল, কুল, বাতাবি গাছের ডালে ডালে ঘটেছে আমার অগ্রগতি। বর্ষার কাদাজলে চলেছে হরদম ফুটবল খেলার অনুশীলন–সেদিন সারাগাঁয়ে মায়ের যে পরশ পেয়েছি সেই পুরোনো কথা ভেবেই কাটাতে হবে বোধ হয় বাকি জীবন। সেদিনের ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ আজও লেগে রয়েছে আমার নাকে।
‘মতরী’ অর্থাৎ মিত্র বাড়ির দাওয়ায় যে দোকানঘরটি ছিল তাতেই সকাল সন্ধ্যায় বসত আচ্ছা। আশপাশের গ্রামের লোকও আসত সওদা করতে, গল্পগুজব করতে। আমাদের গ্রামটি হিন্দুপ্রধান হলেও দোকানঘরের মিলনতীর্থে দেখা মিলত সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষেরই চৌকিদার মুজহরলাল থেকে আরম্ভ করে চোর মরকালী, আর বুড়ো হাফেজ মিয়া থেকে আরম্ভ করে মিয়াদের বিকৃতমস্তিষ্ক বিলেত-ফেরত ছেলেটি পর্যন্ত সেখানে আসত দিনান্তে অন্তত একটিবার। পাগল ছেলেটি আপন মনে বিড়বিড় করে বকলেও ব্যবহারে কোনোরকম পাগলসুলভ হাঙ্গামা করতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। বেত ঘুরিয়ে গুরুমশায়ী চালে যখন সে চলে যেত আমার কিশোর মনে তখন জাগত প্রচন্ড বিস্ময়। সেদিন মানুষকে পাগল হতে দেখেছি, আজ দেখছি গোটা জাতি হয়ে উঠেছে পাগল! এমন পাগলামি করলে শান্তিতে মানুষ থাকবে কী করে সে-চিন্তা কারও মনে জাগেনি আজ পর্যন্ত? মানুষ বাঁচলে তবে তো জাতি,–তবে কেন জাতিবোধের আজ এমন প্রাধান্য মানুষের ওপর? মানুষ কী মরে গেছে? জাতের বজ্জাতি শেষ হোক এই প্রার্থনাই করছে সমস্ত সম্প্রদায়ের সমস্ত মানুষ!
মনে পড়ে বুড়ো তমিজুদ্দিনকে। বুড়ো ঘর ছাইত বছর বছর। সুপারির মরশুমে সুপারি দিত পেড়ে। প্রতি গাছ থেকে তার পাওনা ছিল এক গন্ডা সুপারি। সরু লম্বা একটা বাঁশের মাথায় কাস্তে বেঁধে সুপারি পাড়ত ছোকরাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। শুনেছি বয়সকালে তমিজুদ্দিন গাছে উঠত কাঠ-বেড়ালের মতো, বুড়ো বয়সে আর ভরসা করে না সরু গাছে উঠতে। মনে পড়ে বলীকেও। সে যখন জমিতে মই দিত তখন গিয়ে তার পেছনে কোমর জড়িয়ে মই-এর ওপর দাঁড়াতাম। বেঁটে বুড়ো বাধা তো দিতই না, বরং বাঁদিকের গোরুটার ল্যাজ মুচড়ে হেঁই-হেঁইও বলে আমাকে আনন্দে দেবার ব্যবস্থা করত। কিছুক্ষণ পরে নামিয়ে দেবার মতলবে প্রশ্ন করত, ‘অইল।’ ধুলোয় ধূসরিত শরীরের দিকে তাকিয়ে আমি শুধু জবাব দিতাম—’উঁহু!’
মনে পড়ছে মিত্রবাড়ির ঝুলন উৎসবের কথা। দামামার শব্দে কর্ণপটাহের অবস্থা হত সঙিন। আরতির ধূপের ধোঁয়ার আবছা পরিবেশের মধ্যে দেখতাম ঠাকুর দুলছেন, দোল খাচ্ছেন সহাস্য মুখে। পুজোর আরতিই ছিল সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ব্যাপার। ছেলে বুড়োনির্বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ হয়ে আরতি করত ভক্তিনম্র চিত্তে। বাজনার তালে তালে আরতি উঠত জমে, আগুনের ফুলকি পড়ত ছড়িয়ে এদিক-ওদিকে। ঢুলির বাজনার ছন্দ যখন চরমে, নাচতে নাচতে আরতিকরদের হাত থেকে তখন খসে পড়ত ধনুচি, আগুন ছিটকে পড়ে দু-একজনকে ঘায়েলও যে করত না তা নয়, কিন্তু সেদিকে নজর দেবার মনের অবস্থা তখন কোথায়? এইসব নিয়েই আমার গ্রাম, এইসব অনাসৃষ্টি নিয়েই পূর্ববাংলার সব গ্রাম পরিপূর্ণ। সামান্য ঝুলন উৎসবকে কেন্দ্র করেই যে বিরাট আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা সেদিন যারা করত আজ তারা কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে জানি না।
পুজোর সময় ধরদের বাড়িতে হত উৎসব। অভিজাত বাড়ির নোনা-ধরা দেয়ালের মতো তার সব কিছুতেই নোনা ধরলেও এই সেদিন পর্যন্তও পুজোর আনন্দটা ছিল অকৃত্রিম। ঢপ, রামায়ণ গান থেকে আরম্ভ করে যাত্রাগানের মধ্যে দিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠত সমস্ত গ্রামখানি। রামায়ণ গানের দু-চার লাইন আজও মনে আছে আমার। সেদিনকার আসর-ভরতি লোকের সামনে যখন গায়েন রামের রাজ্যাভিষেকের চিরঅভিপ্রেত সংবাদটি ঘোষণা করতেন তখন দর্শকদের মুখে ফুটে উঠত স্বস্তির হাসি। সে হাসির উৎস ছিল বিশেষ করে এই কথাটি,
ওগো কৌশল্যে, শুনে কী আনন্দ হল অযোধ্যার
রাজা হবে রঘুমণি লক্ষ্মণ হবে ছত্রধারী–
বামে সীতা সীমন্তিনী সদা নিরখি।।
এই যে সুখীসচ্ছল ভবিষ্যৎ অযোধ্যার ছবি, এ ছবি তো চিরন্তন। জীবনের ওপর সার্থকতার ছাপ পড়লে এমন নির্বিঘ্ন ছবি ফুটবে কী করে?
যাত্রার মধ্যে দীনবন্ধুর নাচই ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয়। পুজোর সময় তাকে পাওয়া ছিল দুর্লভ সৌভাগ্যের কথা। বড়ো বড়ো যাত্রার দলে থাকত তার চাহিদা। তার ‘পূজারিনি’ নৃত্যই ছিল সবচেয়ে বিস্ময়কর। মাথায় ও দু-হাতে তিনটি ধূপদানি নিয়ে পূজারিনি তার বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে দেবতাকে অর্ঘ্য নিবেদন করছে, অথচ প্রণাম করতে গিয়েও তার ধূপদানি স্থানচ্যুত হচ্ছে না। তার নৃত্যলালিত্য দেখলে বিশ্বাসই করা যেত না যে শরীরে তার হাড় আছে একটাও! আমাদের গ্রামে দীনবন্ধুই ছিল প্রাচীনকালের সুরুচিসম্পন্ন নৃত্যের ধারক ও বাহক।
আজ ফেলে-আসা দিনগুলির ধূসর স্মৃতিরোমন্থনই ভালো লাগছে। আজ আমাদের অবস্থা মহাভারত বর্ণিত অভিমন্যুর মতো। তবে অভিমন্যু প্রবেশের মন্ত্র জানতেন, বের হয়ে আসার মন্ত্র সম্বন্ধে ছিলেন অজ্ঞ। আমরা বেরিয়ে আসার মন্ত্র জানি, জানি না ছেড়ে-আসা গ্রামে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভের মন্ত্র, এই তফাত! মৈত্রী-সাধনার মধ্য দিয়েই পাওয়া যাবে সে-পথের সন্ধান।
.
সন্দীপ
দক্ষিণে সুন্দরবন, উত্তরে তরাই। বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানা এই। তবু আরও এক মৃত্যুদীপ্ত ইতিহাস ছিল এই সীমানির্ধারিত ভূখন্ডের। সে-ইতিহাস একদিনে গড়ে ওঠেনি। নদীমাতৃক বাংলাদেশের বুকে পলিমাটির স্তরের মতো যুগে যুগে সাত কোটি মানুষের বুকের ভালোবাসায়, অশ্রুতে, প্রতিজ্ঞায় এ ইতিহাস লিখিত হয়েছিল। আজ নিজের হতে সে ইতিহাসকে দ্বিখন্ডিত করে দিলাম। এক সীমান্তের মানুষ আর এক সীমান্তে উপনীত হল শরণার্থীর বেশে, আশ্রয়ের প্রার্থনায়। হায় আমার দেশ! যেখানেই থাকি, যত দূরেই থাকি, এ দেশের মাটিকে, এ দেশের আকাশকে তো ভুলতে পারি না। এ দেশে যে আমি জন্মেছি, এ দেশ যে আমার জননী।
দূর থেকে একটা কালো বিন্দুর মতো মনে হয় প্রথম। সমুদ্রের বুকে বুঝি বা কোনো ভাসমান কাষ্ঠখন্ড। ঢেউয়ের ভেতর ডুবে যাচ্ছে কখনো–আবার মাথা তুলছে হঠাৎ। কর্ণফুলি নদীকে অনেক পেছনে ফেলে সমুদ্রের মোহনায় এসে পড়েছে মোটরলঞ্চ। এবার সোজা কোনাকুনি পাড়ি জমাতে হবে। ঢেউয়ের তালে তালে ভেসে চলেছে লঞ্চ। যান্ত্রিক আর্তনাদ তলিয়ে যাচ্ছে সামুদ্রিক ঢেউয়ের উত্তাল বিক্ষোভে। নির্মেঘ আকাশে মধ্যাহ্নের সূর্য। রোদের স্পর্শে সফেন ঢেউগুলি হিরন্ময় দীপ্তি ছড়িয়ে দিচ্ছে। ইগলের মতো অনুসন্ধানী চোখে তাকালেও উপকূল চোখে পড়বে না আর। শুধু অন্তহীন জল চারদিকে–ঢেউয়ের অবিশ্রান্ত গর্জন। পালতোলা নৌকার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় মাঝে মাঝে। দেখা যায় দু-একখানা যাত্রীবাহী নৌকা। সমুদ্রের উপযোগী বিশেষ ধরনের নৌকা এইসব। দিকচিহ্নহীন সমুদ্রে নৌকারোহীদের একমাত্র সহায় মাঝির অদ্ভুত দক্ষতা আর যাত্রীর দুর্নিবার সাহস। প্রায়ই বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হয় এদের। তবু পরাভূত হয় না এরা, অনেক প্রাণের বিনিময়ে কঠিন অভিজ্ঞতায় শক্তিমান সবাই। তাই রুদ্রের অভিসারে অভ্যস্ত এরা প্রত্যেকে।
দুপুরের সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ে এক সময়। সেই কালো বিন্দুটা চোখের সামনে পরিষ্কার হয়ে দেখা দেয় এইবার। সুপারি, নারকেল গাছে ঘেরা একটুকরো ভূখন্ড। সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে ভূখন্ডের গায়ে। যে-কোনো মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে বলে কিনারে গিয়ে ভিড়ল লঞ্চ। ঢেউয়ের দোলায় লঞ্চ তখন কাঁপছে। কোনো অবলম্বন ছাড়া লঞ্চের ওপর দাঁড়ানো যায় না। আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় খালাসিরা কিন্তু সিঁড়ি ফেলে দিলে। তাদের হাত ধরে ধরে সিঁড়ি পার হয়ে উঠে এল যাত্রীদল। এখান থেকে গন্তব্যস্থল মাইল দুয়েকের পথ। কিন্তু সেখানে যাওয়া যায় কী করে? মোটর, ঘোড়ার গাড়ি, রিকশা কিছুই নেই। একটা কাঁচা রাস্তা এঁকেবেঁকে ভেতর দিয়ে চলে গেছে। ছোটো ছোটো মোট কাঁধে নিয়ে যাত্রীরা কেউ কেউ সেই পথে রওনা হয়। বাকি যারা রইল তারা আশ্রয় নিল গোরুর গাড়ির। যাতায়াতের একমাত্র উপায় এই দ্বিচক্রযান।
নতুন কোনো আগন্তুক তখন হয়তো সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন–সামনে অনন্ত সমুদ্র, দিগন্ত চোখে পড়ে না। একটা ঝলসানো তাম্র পাত্রের মতো পশ্চিমের সূর্য সমুদ্রের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। নিজের অস্তিত্ব লুপ্ত করে দেবার কামনায় উদবেল বিকেলের সূর্য। আশপাশের গাছগুলোতে পাখিদের ক্লান্ত কলরব। একটা স্তব্ধ বিষণ্ণ পরিবেশ। মুহূর্তের জন্যে অবাক হয়ে যান আগন্তুক। বাংলাদেশের অংশ নাকি এটা? কিন্তু বাংলার কোনো অঞ্চল এমন দুরধিগম্য, বহির্জগৎ-বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে ভাবতে পারেননি ভদ্রলোক। একটা বিস্মিত চেতনায় কয়েক মুহূর্ত কেটে যায়। পাশে দাঁড়িয়ে গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান যে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছে। সেদিকে খেয়ালই নেই তাঁর।
প্রায় দেড়শো বছর আগে একদল লোক যেদিন এখানে এসে নেমেছিল সেদিন তারাও বোধহয় বিস্মিত চোখে তাকিয়েছিল কিছুক্ষণ। কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল তাদের নির্ধারিত। কর্তব্য ছিল সুপরিকল্পিত। সাতসমুদ্র তেরো নদী পার হওয়া রূপকথার রাজকুমারের মতো তাদের চমকপ্রদ অভিযাত্ৰা তাই থেমেছিল এখানে। জাতে ছিল তারা পোর্তুগিজ। পসরা খুলতে দেরি হয়নি তাদের। অপ্রতিহত আধিপত্যে বাঁধা পড়েনি কোথাও। দেড়-শো বছর আগে বাংলার প্রত্যন্তভাগের এই দ্বীপটিও ঔপনিবেশিক আলোর সংস্পর্শ থেকে অব্যাহতি পায়নি। ইতিহাসে তবু এই দ্বীপটির কথা হয়তো দেখতে পাবেন না, কারণ বিশেষজ্ঞের গবেষণার বাইরে যে এই দ্বীপ–আমার দেশ এই সন্দীপ।
শহরের অংশটিকে বলা হয় হরিশপুর, অবশ্য ঠিক শহর নয়। একটি থানা, মুনসেফ আদালত আর সাবট্রেজারি অফিস গোটা দ্বীপটার শাসনব্যবস্থার প্রতিভূ। মাইলখানেক পরিধি শহরের। দক্ষিণদিকে দিঘিরপাড় অঞ্চল জুড়ে অধিকাংশ শহরবাসীর বাস। একটা বিরাট দিঘির চারদিকে ছোটো ছোটো ঘর। কোনোটার চালা টিনের, কোনোটার বা খড়ের। কবি নবীন সেন যখন মুনসেফ ছিলেন এখানে তখন তাঁরই উদ্যমে কাটানো হয়েছিল এই দিঘি।
দিঘিরপাড়েরই বাসিন্দা ছিলাম আমি। দিঘির জলে সাঁতার কাটা একটা অপরিহার্য আনন্দের অঙ্গ ছিল আমাদের। তা ছাড়া আরও একটা কারণে দিঘিটি আকর্ষণীয় ছিল শৈশবে। ছোটো ছোটো রঙিন মাছ দিঘির কিনারে শ্যাওলা ঝোঁপের ভেতর ঘুরে বেড়াত। পাঠশালা পালিয়ে দল বেঁধে সেই মাছ ধরতে আসতাম আমরা। বড়োদের চোখ এড়িয়ে নিষিদ্ধ কাজটা সেরে নেবার সেই ছিল সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু সময় সময় ধরা পড়ে যেতাম তবু।
‘ওখানে কী করছিস তোরা?’–-একদিন একটা গম্ভীর গলার আওয়াজ শুনে হকচকিয়ে চেয়ে দেখি সুধেন্দুদা দাঁড়িয়ে পেছনে। পড়ি কি মরি করে যে যেদিকে পারল ছুটে পালাল, ধরা পড়ে গেলাম আমি।
পাঠশালা পালিয়ে এই কাজ করে বেড়াচ্ছিস? সুধেন্দুদা তখনও আমার হাতটা ধরে রেখেছেন। আমার মুখে ‘টুঁ’ শব্দটি নেই।
‘দিঘির পাহারাওলা দেখতে পেলে হাড় ভেঙে দেবে সে খেয়াল আছে?’–সুধেন্দুদা হাত ছেড়ে দিয়ে কাছে টেনে নিলেন আমাকে। নিবিড় স্নেহে দু-হাতে জড়িয়ে ধরলেন। একটা প্রীতির প্রবাহ যেন এই সুধেন্দুদা। বিদেশি যুগের জেলখাটা লোক। বাড়ি মাইটভাঙা গ্রামে। শহরে ছোটো একটা বইয়ের দোকান আছে তাঁর। স্কুল-পাঠশালার বই ছাড়াও উঁচুদরের সব বই রাখতেন তিনি। ওসব বই কাউকে কিনতে দেখিনি কখনো। সুধেন্দুদা আমাদের পড়তে দিতেন বইগুলো। রাজনীতি আর সাহিত্যের আস্বাদ নিতাম আমরা সেইসব বই থেকে। ঝড়ের রাতের বিজয়ী অশ্বারোহীর মতো আজও দেখতে পাই সুধেন্দুদাকে। মাইটভাঙায় চিরাচরিত দুর্গাপুজো নিয়ে জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল একবার। হিন্দু-মুসলমানের উন্মত্ত বিরোধ, দু-পক্ষই কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছে। একটা রক্তের নদী হয়তো বয়ে যাবে কিছুক্ষণ পরেই। সহসা সুধেন্দুদা কোথা থেকে এসে মাঝখানে বাজের মতো পড়লেন। বিরোধের নিষ্পত্তি হল নিমেষেই। কিন্তু আঘাতে জর্জরিত হয়ে অচেতন অবস্থায় হাসপাতালে চলে গেলেন সুধেন্দুদা। সেই অনির্বাণ আদর্শের দীপশিখাকে ভুলব না কোনোদিন।
রবিবার আমাদের কাছে ছিল একটা দুর্লভ দিন। দুপুরের পরেই বেরিয়ে পড়তাম আমরা। আমাদের দলের সর্দার ছিলেন দ্বিজেনদা। শহরের বুকের ওপর দিয়ে সোজা উত্তর দিকে যে রাস্তাটা চলে গেছে সেই পথে হেঁটে চারআনির বাগে চলে যেতাম আমরা। দুর্গম জঙ্গলে আচ্ছন্ন চারআনির বাগ। সরু সরু পায়ে হাঁটা পথ আছে ভেতরে ঢুকবার। কয়েকটি পুরোনো দিঘি নানানরকম জলজ গুল্মে এমনভাবে ঠেসে আছে যে সেইসব আগাছার ওপর দিয়ে স্বচ্ছন্দে হেঁটে পার হওয়া যায়। জঙ্গলের এখানে সেখানে দালানের ধ্বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে।
একটা কাহিনি প্রচলিত আছে এই চারআনির বাগ সম্বন্ধে। পোর্তুগিজদের বিলীয়মান প্রভাবের মুখে মুসলমান কৃষাণের ছেলে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিল সন্দীপের। প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে নাম নিয়েছিল সে দিলাল রাজা। বাগানের এই জায়গায় ছিল তার রাজপ্রাসাদ। তারপর একদিন দিলাল রাজার ক্ষমতাও অপহৃত হল আর কালক্রমে তার প্রাসাদ পরিণত হল এই জঙ্গলাকীর্ণ বাগানে। পায়ে হাঁটা পথ থাকলেও বাগানে বড় একটা ঢোকে না কেউ। কাঠুরেরা কাঠ কাটতে আসে মাঝে মাঝে। আর আসে গ্রামাঞ্চলের নামকরা সাপুড়ে ওঝারা। সাপ ধরবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তাদের। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিষধর সাপ ধরে ফেলে–বৃহৎ অজগরও অনায়াসে আয়ত্তে নিয়ে আসে। এইসব সাপ শহরে গ্রামে দেখিয়ে পয়সা রোজগার করে তারা। বাগানের একটু দূরেই চারআনির কাছারিঘর। কাছারিঘরের সামনেই খোলা মাঠে হাট বসে শনি-মঙ্গলবার। হাটের এই দুইদিন নিস্তেজ নিষ্প্রাণ চারআনি হঠাৎ জেগে ওঠে যেন। সহস্র লোকের পদাঘাতে ও পদপাতে চারআনির বুকে প্রাণ সঞ্চার হয়। শুক্রবারে চাঁদবিবির মসজিদে নামাজের জমায়েত বসে। কাছারির ডান দিকে একটা বড়ো পুকুরের পাড়ে চাঁদবিবির মসজিদ। কারুকার্য খচিত, হলদে রঙের বিরাট মসজিদ। অনেক কালের পুরোনো। ইতিহাসের চাঁদ সুলতানা এর নির্মিতা বলে সন্দেহ করে অনেকে।
পড়ন্ত রোদে ধুলো মাখা-গায়ে অন্য কোনো পথে ফিরতাম আমরা। হাঁটতে হাঁটতে বসে জিরিয়ে নিতাম পুন্নাল গাছের স্নিগ্ধ ছায়ায়। অশ্বথ বটের মতো বিশালকায় গাছ। শাখাপ্রশাখায় অজস্র গুটি ফল ধরে। গ্রামের লোকেরা এই ফল থেকে একপ্রকার তেল তৈরি করে বাতি জ্বালায়। পুন্নালের ছায়া ছাড়িয়ে এসে দাঁড়াতাম হাওতালের পুলের ওপর। পুলের নীচে একটা খরস্রোতা খাল। কৃষাণের ছেলেরা মহিষের পিঠে চড়ে ওপারে গিয়ে ওঠে।
মন আজ মুখর হয়ে উঠেছে স্মৃতিতে। কালবৈশাখীর আসন্ন ঝড়ের সংকেতে সন্দীপের সমুদ্র হয়তো এখন গম্ভীর হয়ে উঠেছে। অপর পারের যাত্রীদের পক্ষে এ সময়টা ভয়ংকর, তবু এই ভয়ংকরের রুদ্র লীলার চরণতলে দোদুল্যমান সন্দীপের চরকে ভুলতে পারিনি। যদি কোনোদিন সুযোগ আসে আবার ফিরে যাব। আবার মন খুলে বঙ্গোপসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে নীলাঞ্জন আকাশের দিকে মুখ তুলে গাইব–’সার্থক জনম মাগো, জন্মেছি এই দেশে।
পাবনা জেলা – গাড়াদহ পঞ্চকোশী ঘাটাবাড়ি সাহজাদপুর
কালের চাকা আবর্তিত হয়ে চলেছে অবিরাম। মানুষের জীবনের ওপর সে চাকার দাগ স্পষ্ট হয়ে থাকে। তাই একদিন যারা ছিল শ্যামল মায়ের আদুরে দুলাল, প্রকৃতি তার হৃদয়ের সমস্ত সৌন্দর্য নিঙড়ে যাদের অন্তর করেছিল কোমল, সজীব, তারা আজ রিক্ত, সর্বহারা। তারা কি কখনো ভেবেছিল, যে-দেশকে তারা ‘মা’ বলে জেনেছে–যে-দেশের মাটি তাদের কাছে স্বর্গের চেয়েও পবিত্র, সেই দেশ তাদের নয়? একটা কালির আঁচড়ের ফলে তাদের সব কিছু ছেড়ে আসতে হবে? ওপারের লক্ষপতি এপারে আসবেন শরণার্থী হয়ে, একটু মাথা গোঁজবার ঠাঁই আর দু-মুঠো ভাতের জন্যে হবেন অন্যের কৃপাপ্রার্থী। কচি শিশুর মুখে তুলে দেবেন দুধের গুঁড়ো? বাস্তবের কঠিন কশাঘাতে মন যখন নিস্তেজ হয়ে আসে তখন মনে পড়ে পল্লির সেই অনাবিল সৌন্দর্যের ছবি। মানসপটে ভেসে ওঠে দিগন্ত বিস্তৃত সেই শ্যামল বনানীর শোভা। কিন্তু সে রামধনুর মতোই ক্ষণস্থায়ী। তবুও তাকে তো ভোলা যায় না। ছন্নছাড়া জীবনের লক্ষ্যহীন যাত্রাপথে সেই ছবিই বার বার ভেসে ওঠে। আমার গ্রাম আমাকে ডাকে–নিভৃতে, অতিগোপনে। তার সেই ডাকে কি আর কোনোদিনই সাড়া দিতে পারব না? তার গোপন আহ্বান কি কোনো সাড়া না নিয়েই ফিরে যাবে?
পাবনা জেলার একটি ছোট্ট গ্রাম, গাড়াদহ তার নাম। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন পটে আঁকা একখানা ছবি। শীর্ণকায়া করতোয়া কুলু কুলু রবে গাঁয়ের পূর্বসীমানা দিয়ে বয়ে চলেছে।
প্রায় পাঁচ হাজার লোকের বাস আমাদের গাঁয়ে। তার মধ্যে অর্ধেকের বেশি মুসলমান। অধিকাংশেরই জমিজমা বেশি নেই। অন্যের জমি বর্গা নিয়েই এরা সংসার চালায় আর সকলের আহার জোগায়। সারাদিন এরা হাড় ভাঙা খাটুনি খাটে। শেষরাতে পাখির ডাকে এদের ঘুম ভাঙে। কাঁধে লাঙল নিয়ে তখন দলে দলে সবাই মাঠে যায়–সঙ্গে নিয়ে যায় এক বদনা জল আর তামাক–যা না হলে এদের একদন্ডও চলে না। মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করে আবাদের খরচ জোগায়। সবসময় এক চিন্তা–কী করলে ফসল ভালো হবে। ভগবানের কাছে মানত করে ঠিক সময় বৃষ্টি দেওয়ার জন্যে। বর্ষায় গ্রামের অলিগলি পুকুর যখন কানায় কানায় ভরে ওঠে, নৌকা ছাড়া যখন ঘর থেকে বের হওয়া যায় না তখনও দেখেছি ওরা দলবেঁধে ডুব দিয়ে দিয়ে পাট কাটছে। সমস্ত মাঠ ওদের কণ্ঠনিঃসৃত ভাটিয়ালি গানে মুখর হয়ে উঠেছে। ওদের চোখে মুখে ফুটে ওঠে অনির্বচনীয় আনন্দোচ্ছাস। ওরা বলে, ওই গানের সুরের মধ্যেই সব কষ্ট ভুলে থাকার মন্ত্র রয়েছে। ওদের অনেকের বাড়িতেই তেমন ভালো ঘর নেই। কোনোরকমে বেঁচে থাকার জন্যে যা প্রয়োজন তার বেশি কিছুই নেই। অনেকে শুধু মজুর খেটেই সংসার চালায়। আবার কেউ কেউ ছোটোখাটো ব্যাবসাও করে। দল বেঁধে ওরা হাটে যায়। মাছ, লঙ্কা, পেঁয়াজ এগুলো না হলে একদিনও ওদের চলে না। সুখ-দুঃখের আলাপ করতে করতে বাড়ি ফেরে। আশ্বিন-কার্তিক মাসে যখন ধানের খেতে সোনার রং দেখা দেয়, বাতাসে ধানের শিষগুলো নুয়ে পড়ে যখন পথচারীকে সাদর সম্ভাষণ জানায়, তখন চাষিদের মনে আর আনন্দ ধরে না। ধানখেতের দিকে চেয়ে তারা বৎসরের সমস্ত কষ্ট ভুলে যায়। কবে তারা এই ধান ঘরে তুলবে? এ থেকে দিতে হবে মহাজনের দেনা, ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্স, জমিদারের খাজনা, আরও কত কী!
উত্তর দিকে তাঁতিপাড়া। দিন-রাত খটখট শব্দে তাঁত চলছে। গামছা, লুঙ্গি, ছোটো কাপড় –এগুলোই সাধারণত বোনা হয় ওদের তাঁতে। সপ্তাহে একদিন করে তাঁতিরা হাটে তা নিয়ে যায়, মুনাফা যা থাকে তাতে ভালোরকমেই চলে। রাস্তা দিয়ে চলতে নতুন সুতোর কেমন যেন একটা গন্ধ নাকে আসে। কোনোসময়ই তাঁত বোনার বিরাম নেই। তাঁতিপাড়ার একটু দূরেই কুম্ভকারদের বাস। কত সময় গিয়ে বসেছি ওখানে। কী নিপুণ হাতের স্পর্শে কাঠের ঘূর্ণায়মান চাকার মাঝ থেকে হাঁড়ি তৈরি হয়ে আসত তা দেখে আশ্চর্য হতাম। এরপর সেইসব হাঁড়ির সঙ্গে বালি মিশিয়ে তারা পিটত অতিসন্তর্পণে। রাশি রাশি হাঁড়ি, কলসি, থালা, বাটি একসঙ্গে জড়ো করে মাটির নীচে গর্ত করে তার ওপর মাটি চাপা দিয়ে ভেতর থেকে আগুন ধরিয়ে দিত। বুড়িতলা’য় মানত করত যাতে এ সময় বৃষ্টি না হয়। পুজো-পার্বণ উপলক্ষে কুমোরপাড়ায় লোকের ভিড় জমত। সবাই দেখেশুনে বাছাই করা জিনিস নিয়ে আসত। পরিশ্রমের তুলনায় সে জিনিসের দাম নিতান্তই কম। বর্ষার সময় নৌকো বোঝাই করে কুমোররা এগ্রাম সেগ্রাম ঘুরে বেড়াত এবং হাঁড়ি-কলসির বিনিময়ে গৃহস্থের বাড়ি থেকে ধান নিত। এইটেই ছিল ওদের বড়ো আয়। এইভাবে তারা সারাবছরের ধান জোগাড় করে রাখত।
আর একটু দূরেই কর্মকারপাড়া। এখানেও সারাদিনরাত হাতুড়ির আওয়াজ কানে আসত। বিয়ে বা অন্য উৎসব উপলক্ষ্যে এদের কাজ বহুগুণ বেড়ে যেত। কোনো চাষিরই প্রায় সোনার গয়না তৈরি করার সামর্থ্য নেই। তাই পাটের টাকা পেলেই তারা বৎসরে অন্তত একটিবার রুপোর গয়না তৈরি করায়। সবচেয়ে ভিড় জমত সাধুর দোকানে। রাত্রিতে লাল টকটকে লোহার চিমটে দিয়ে ধরে সে যখন গয়না পিটত তখন চারদিকে আগুনের ফুলকি উড়ে পড়ত। আর সেই জ্বলন্ত লোহার আঁচে তার মুখের একাংশ লালচে মেরে যেত। এই। কর্মচঞ্চল জীবনের মাঝখানেও এরা আমোদ-প্রমোদ অত্যন্ত ভালোবাসত। মাঝে মাঝে খোল করতাল নিয়ে কীর্তন করত; আবার কবিগান, পাঁচালি, ঢপ কীর্তন, কৃষ্ণযাত্রা, বাউলগান শুনেও কোনো কোনোদিন রাত কাটিয়ে দিত। খাবারের চিন্তা তাদের ছিল না, তারা জানত যতদিন হাত ততদিন ভাত, তাই অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে তারা থাকত না।
কেউ অন্যায় করলে তার বিচার হত গ্রামেই। হিন্দুপ্রধান এবং মুসলমান প্রধানদের নিয়ে বসত পঞ্চায়েত। আসামি নত মস্তকে তাঁদের নির্দেশ মাথা পেতে নিত। সুখে দুঃখে সকল সময়ে এমনিভাবে গ্রামবাসীরা একসঙ্গে বসে তাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করেছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরের সময়ও ঠিক এমনিভাবে তারা তাদের কর্মপন্থা ঠিক করেছিল। জমিদারবাড়িতে দরবার বসল। সামনেই একটা ছোটো চৌকির ওপর তাকিয়া হেলান দিয়ে তিনি বসে রয়েছেন। সামনে হুঁকোর নলটি পড়ে আছে। গ্রামের প্রধানগণ একে একে এসে তাঁকে নমস্কার জানিয়ে যে যার আসনে বসে পড়ল। প্রজাদের সুখ-দুঃখের অভিভাবক তিনি।
গ্রামের ঠিক মধ্যস্থলে রায়েদের বাড়ি। পাশেই ব্রাহ্মণপাড়া, পুজোআর্চা নিয়েই এরা সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। সন্ধের সময় প্রতিবাড়িতে ঠাকুরের সন্ধ্যারতি আরম্ভ হত। মন্দিরপ্রাঙ্গণ লোকে ভরে উঠত। ছেলে-মেয়েরা পুজোর প্রসাদ নিয়ে বাড়ি ফিরত। এ ছিল তাদের নিত্যকর্ম। রায়েদের বাড়ির সামনেই খেলার মাঠ। শত কাজের মধ্যেও দলে দলে লোক আসত খেলা দেখতে। অনেক দূর থেকেও খেলোয়াড়গণ আসত। গ্রামবাসীরা তাদের সেবার ভার সানন্দে নিজেদের মাথায় তুলে নিত।
মাঠের একপাশেই ‘বুড়িতলা’। কীভাবে যে এর এই নামকরণ হয়েছে তা আমরা জানি না। প্রতিশনিবার এর প্রাঙ্গণে লোক সমাগম হত। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নর-নারী হাতে পুজোর ডালা নিয়ে বসত এই বুড়িতলায়। আসলে গাছটা ‘সরা গাছ। গোড়া থেকে দু-তিন হাত পর্যন্ত সিঁদুর দিয়ে লেপা। লোকে বলে এ গাছ নাকি জ্যান্ত দেবতা। লোকমুখে আরও শোনা যায় যে, আশপাশের অন্ধকারে কারা নাকি ঘুরে বেড়ায়।
গাঁয়ের পূর্ব দিকে নদীর ধারে জেলেদের বাস। বর্ষার শীর্ণকায়া করতোয়া যখন কানায় কানায় ভরে ওঠে, জেলেদের ডিঙি তখন সমস্ত নদী ছেয়ে ফেলে। নদীর এপার থেকে ওপার
পর্যন্ত মোটা মোটা বাঁশ পুতে দেওয়া হয় এবং মাঝে কিছুটা জায়গা ফাঁকা থাকে। তারপর সমস্ত জায়গাটা জেলেরা জাল দিয়ে ঘিরে দেয়। বর্ষার সময় এইরকম ভাবে জেলেদের জালে বড়ো বড়ো মাছ ধরা পড়ে। গ্রামের হাটে এদের ধরা মাছ বিক্রি হয়। লোকের ভিড় খুব বেশি হলে উৎসাহী হয়ে হয়তো অমুক সর্দার কি পরামানিক তাকে মাছ বিক্রি করে ঠিকমতো দাম নিতে সাহায্য করে। বেচা-কেনা শেষ হলে জেলেরা খুশি মনে এদের হয়তো একটা ভালো মাছ খেতে দেয়। এর মধ্যে কোনো কুটিলতা নেই। অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে, সহজ অন্তরে এরা সাহায্যকারীকে তার পরিশ্রমের জন্যে সামান্য কিছু উপহার দেয়।
খেলার মাঠের একটু দূরেই স্কুল, ডাকঘর, ইউনিয়নবোর্ড অফিস। ডাকঘর থেকে যে রাস্তাটা সোজা চলে গেছে ওই রাস্তার পাশে থাকত এক বাগদি নাম তার ঝন্টু। ডান হাতের কবজি পর্যন্ত কাটা। ওর নাকি আগে মাছ ধরার খুব ঝোঁক ছিল। গাঁয়ের পশ্চিম দিক দিয়ে যে বিলটা গেছে লোকে আজও ওটাকে ‘লক্ষমণির বিল’ বলে। ঝন্টু একদিন নাকি ওখানে মাছ ধরতে যায় গভীর রাত্রিতে। ঝুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়ছে। হঠাৎ দেখল সাতটা কলসি ভেসে আসছে–আর তার ভেতর থেকে ‘টুং টাং’ আওয়াজ হচ্ছে। প্রথম কলসিটি ধরতেই সে শুনতে পেল কে নাকি ভেতর থেকে বলছে-‘তোমার যা দরকার পরের কলসিটি থেকে নাও। এইভাবে পর পর ছয়টি চলে গেল। শেষের কলসির ঢাকনাটা আপনা থেকেই খুলে গেল। কে নাকি বলল–’একবারে যা পারো নাও। ঝন্টু দেখল ঘড়া ভরতি সোনার মোহর– একবার নিয়ে কোঁচড়ে রেখে আবার যেমনি হাত দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে হাতের কবজিটুকু কলসির ভেতরেই রয়ে গেল। সেই থেকে নাকি ও ‘হাতকাটা ঝন্টু’ বলেই সকলের কাছে পরিচিত।
এখন বৃদ্ধ হয়ে গেছে ঝন্টু। তবু সে মাঝে মাঝে গ্রামের মধ্যে নানারকম খেলা দেখিয়ে বেড়ায়। কোনোদিন বা গান গায় আবার কোনোদিন বা নিজের জিভটা কেটে থালার ওপর রেখে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। ছেলেবেলায় ওর কারসাজি না বুঝতে পেরে অবাক বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকতাম।
পুজোর সময় আমাদের গ্রাম এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করত। আনন্দময়ীর আগমনে চারিদিক আনন্দমুখর হয়ে উঠত। আমাদের পেয়ে গাঁয়ের চাষি সম্প্রদায় যেন হাতে স্বর্গ পেত। তাদের ধারণা–আমরা এলেই থিয়েটার হবে। সাড়া পড়ে যেত গ্রামে। এখানে হিন্দু-মুসলমানে কোনো ভেদ নেই। এ যে আমাদের জাতীয় উৎসব-এর সঙ্গে রয়েছে যে আমাদের অন্তরের যোগ। তাই একই সঙ্গে মন্দিরের সামনে ভিড় জমে উঠত হিন্দু-মুসলমানের। কোনো দ্বিধা নেই–কোনো সংকোচ নেই। সকলেই যেন ওই একই মায়ের সন্তান। বিজয়ার দিন করতোয়ার তীর আর একবার ভরে উঠত। উচ্চ-নীচ, ধনী-নির্ধন সব সেদিন এক হয়ে যেত।
গ্রামের দক্ষিণ দিকে বাজার। নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিসই এখানে পাওয়া যায়। গরিব চাষিরা বাড়ি থেকে দুধ নিয়ে আসে বিক্রি করতে। যা পায় তাই দিয়ে অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যাদি কিনে নিয়ে যায়। দুধ খাবার মতো সামর্থ্য তাদের অনেকেরই নেই। বাজারের একধারে বিরাট গর্ত। ওখানে চড়কের গাছ পোঁতা হয়। চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে এখানে মেলা বসে। দেখেছি দু-জনের পিঠে বড়ো বড়ো বঁড়শি বিধিয়ে একটা বাঁশের দু-ধারে ঝুলিয়ে তাদের ঘোরানো হত। সমস্ত শরীর কাঁটা দিয়ে উঠত দেখে। আজ নানারূপেই মনে পড়ছে আমার গ্রামকে। জন্মভূমি থেকে বহুদূরে চলে এসেছি; তবু মনে পড়ছে পাবনা জেলার ছোটো সেই অখ্যাত পল্লি-জননীকে। এখন হয়তো শীর্ণকায়া করতোয়া। বর্ষার প্লাবনে যৌবন উছলা হয়ে উঠেছে। গ্রামের দিগন্তে জমেছে সন্ধ্যার ছায়া। আমার শত স্মৃতি জড়ানো সেই গাড়াদহ। দেশের সীমানায় সে আজ কতদূর, তবু মনের কত কাছে, কত নিভৃতে। এ তারই অশ্রুসজল ইতিহাস।
.
পঞ্চকোশী
পঞ্চকোশী। নদী নয়, গ্রামের নাম। আমার নিজের গ্রাম। নামের হয়তো ইতিহাস আছে। সবটা আজ মনেও নেই, থাকবার কথাও নয়। তবু পাবনা জেলার উপান্তে সিরাজগঞ্জ থেকে পাঁচক্রোশ দূরের এই গ্রামে আমার জন্ম। নামের ইতিহাস যাই হোক, গ্রামটি যে এককালে নেহাত ছোটো ছিল না তার প্রমাণের অভাব নেই। তার পুরোনো আভিজাত্যের পরিচয় পাওয়া যায় নানা কাহিনি বিজড়িত কতকগুলো পরিত্যক্ত ভিটে থেকে; আর পাওয়া যায় হৃতগৌরব জমিদারবাড়ির চুনকাম খসা, নোনাধরা ইটের তিনতলা দালানের চোরা কুঠরির গহ্বর থেকে সেখানে এখন চামচিকে আর লক্ষ্মীপেঁচার তত্ত্বাবধানে পড়ে রয়েছে। রৌপ্যনির্মিত আসা-সোঁটা, বল্লম আর বিরাট আকারের সব ছাতি আর বস্তাপচা অজস্র শামিয়ানা, তাঁবু আর শতরঞ্চি। জীবনের যে সময়টা রূপকথা শোনবার বয়েস সে সময়ে এমন কোনো সন্ধ্যা বাদ যায়নি যেদিন ঠাকুমার মুখ থেকে শুনতে পেতাম না আমাদের গ্রামের প্রাচীন নানা অপরূপ ঐতিহ্যের কাহিনি।
গ্রামের পুবদিকে মাঠের মধ্যে ওই যে একটা ভিটে আছে যেখানে এখন রয়েছে ঘনসন্নিবিষ্ট আমগাছ আর বাঁশের ঝাড়, ওইখানে ছিল মনমোহন দাশের বাড়ি। মনমোহন দাশের ঐশ্বর্যের খ্যাতি ছিল প্রচুর–বদান্যতার খ্যাতি ছিল প্রচুরতর। সেকালের রাজর্ষি জনক রাজা হয়েও নিজহাতে হলকর্ষণ করতেন, আর একালের মনমোহন দাশ সোনার খড়ম পায়ে দিয়ে নাকি নিজে গোরু দিয়ে ধান মাড়াতেন। হয়তো এ নিছক কাহিনি ছাড়া আর কিছুই নয় কিন্তু ঠাকুমার মুখে সেদিন এসব শুনে আমাদের মনে যে অভূতপূর্ব ভাবের সঞ্চার হত সে তো আজও ভুলবার নয়। এমন আরও কত টুকরো টুকরো কাহিনি–! তারপর জমিদারবাড়ির কথা যে বাড়ি একদিন ছিল আত্মীয়-অনাত্মীয়, চাকর-চাকরানির কলরবে মুখরিত, আজ সে বাড়ির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে দাঁড়কাকের কর্কশ কণ্ঠস্বর। এখনও কত নৈশ নিস্তব্ধতার অবকাশে ঠাকুমার মুখে শোনা জমিদারবাড়ির কাহিনি চলচ্চিত্রের মতো একে একে চোখের সামনে ভেসে উঠতে থাকে। জমিদার দীননাথ দাশগুপ্ত তাঁর দিনাজপুরের বাসা থেকে বৎসরান্তে একবার দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে পঞ্চকোশীর বাড়িতে ফিরে আসছেন। সাতদিন আগেই বাড়িতে খবর পৌঁছে গেছে। নায়েব গোমস্তা থেকে আরম্ভ করে পেয়াদা চাকর চাকরানিদের একমুহূর্ত বিশ্রাম নেই। ঘর-দোর ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করার জন্যে সকলেই অতিমাত্রায় ব্যতিব্যস্ততদারক রত নায়েব প্রসন্ন ভট্টাচার্যমশাই তাঁর সুপুষ্ট উদর নিয়ে দোতলা-একতলা ছুটোছুটি করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছেন, আর অযথা চেঁচিয়ে সারাবাড়িটা তোলপাড় করে তুলেছেন। বাইরের মন্ডপে চার-পাঁচজন কুমোর অক্লান্ত পরিশ্রমে সুবিশাল দেবীপ্রতিমা সমাপ্ত করবার জন্যে ব্যস্ত। সকলেই জানে তাদের সবার জন্যেই আসছে নানারকমের উপহার। এদিকে জমিদার দিনাজপুর থেকে জলপথে গ্রামের সীমান্তে এসে পৌঁছেছেন, খবর আসতেই তাঁকে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্যে দলে দলে ছুটে চলেছে হিন্দু-মুসলমান প্রজার দল। প্রত্যেকের কাঁধে একটা করে লাল ব্যাজ–আর হাতে লাল নিশান। পেয়াদা বরকন্দজরাও চলেছে। কাঁধে তাদের রুপোর আসা-সোঁটা, হাতে তাদের রুপোর বল্লম, আর অপরূপ সাজে সজ্জিত বেহারার দল নিয়ে চলেছে বহুবর্ণে খচিত মখমলের জাজিম বিছানো পালকি।…পুজোর কয়েকদিন কারও বাড়িতে হাঁড়ি চড়ত না, হিন্দু মুসলমান সকলেরই সে ক-দিন জমিদার বাড়িতে নিমন্ত্রণ। কল্পনার চোখে দেখতে পাই বাইরের প্রাঙ্গণে সারি সারি পাশা-পাশি বসে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে নিমন্ত্রিত প্রজার দল গরদ বসন পরিহিত নগ্নপদ জমিদার দীননাথ নিজে উপস্থিত থেকে তদারক করছেন তাদের আহারের।…আজ ভাবি সেদিন কোথায় বা ছিল দুই জাতিতত্ত্ব, কোথায়ই বা ছিল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ! পরিপূর্ণ প্রীতির সম্পর্ক ছিল হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে; চাচা, ভাই সম্বোধনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল একটা নিকট মধুর সম্পর্ক! ঝগড়া বিবাদ হত, মারামারি হত–দুই পক্ষই ছুটে আসত জমিদারের কাছারিতে, গ্রামের মোড়লদের নিয়ে বসত মিটিং, হত বিচার, কমিটি যে রায় দিত, দুই পক্ষই তা মাথা পেতে মেনে নিত। হিন্দু সেদিন মুসলমানের কাছে অপরাধ স্বীকার করতে সংকোচ বোধ করত না, মুসলমানও হিন্দুর কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা ভিক্ষে করতে দ্বিধা করত না।
এই তো সেদিনের কথা! মধ্যাহ্নে জমিদারবাড়ির কুল-বিগ্রহের ভোগশেষে যখন কাঁসর বাজত, দেখতাম দলে দলে উল্লসিত কণ্ঠে চিৎকার করতে করতে থালা হাতে ছুটে আসছে হিন্দু-মুসলমান ছেলে-মেয়ে–সকলেই প্রসাদপ্রার্থী। আবার সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠতেই আসত বহু মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ কারও-বা মাথাধরা, কারও-বা চোখ ওঠা, কারও-বা পেটকামড়ানি, কারও বা মেয়েকে ভূতে পেয়েছে–সকলেই আসত একটু ‘ঠাকুর’ ধোয়া পানির জন্যে, (চরণামৃতকে তারা বলত ঠাকুরধোয়া পানি)। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, ‘আচ্ছা মতির মা, তোমরা মুসলমান হয়ে আমাদের হিন্দুর দেবতাকে বিশ্বাস করলে তোমাদের ইসলাম বিপন্ন হয় না?’ মতির মা উত্তর করেছিল, ‘অতশত বুঝি না বাপু, যাতে কইর্যা আমাগো উপগার হয় আমরা তাই করি। তা ছাড়া আপনাগ ঘরে দ্যাবতা, আর আমাগ ঘরে আল্লা আর পেরথক না, আপনারা কন ভগবান আর আমরা কই খোদা!’ সেদিন দেশের অধিকাংশ জনসাধারণই ছিল বোধ হয় আমাদের এই মতির মার মতো মানুষ! সরল অকপট বিশ্বাস নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে তাই তারা হয়ে উঠতে পেরেছিল একাত্ম!
আজ মনে পড়ে সেই নাজির ভাইয়ের কথা। শৈশব থেকে আরম্ভ করে কৈশোর পর্যন্ত প্রতিটি দিনের সে ছিল আমাদের নিত্যসঙ্গী। সামাজিক মর্যাদা, বয়সের পার্থক্য, শিক্ষার স্তরভেদ কিছুই তার ও আমার অভিন্ন হৃদয় বন্ধু হওয়ার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। খেলার মাঠ থেকে আরম্ভ করে পড়ার ঘর পর্যন্ত তার সঙ্গ ছিল আমাদের অপরিহার্য। মনে পড়ে আমির ভাই, ফজু ভাই, জোমসের আলি, আবদুল সরকারের কথা। সন্ধেবেলা মামার ডিসপেন্সারি’ ঘরে কড়া শাসনে তিন-চারজনে মিলে আমরা যখন সুর করে স্কুলের পড়া তৈরি করতাম সময় সময় মামাকে কেন্দ্র করেই আমাদের আড্ডাও জমে উঠত প্রবলভাবে! সন্ধে সাতটা থেকে রাত এগারোটা অবধি কোনো কোনোদিন একটানা আড্ডা চলত। খাবার তাগিদ দিতে দিতে বাড়ির সবাই বিরক্ত হয়ে উঠত, তবু আমাদের আসর চলত পুরো দমে।
মনে পড়ে সেইসব বাল্যবন্ধু রশি, সওকত, রউফদের কথা। নিজেদের গ্রামে হাই স্কুল ছিল না। পড়তে যেতাম দু-মাইল দূরে সলপ স্কুলে। স্কুলে যাওয়ার পথে আমাদের বাড়ি ছিল ‘সেন্টার। দক্ষিণপাড়া থেকে আসত রশিদের দল, আর পাশের গ্রাম রায়দৌলতপূর থেকে আসত সুনীলদা, কার্তিকদা, শান্তি। একসঙ্গে স্কুলে যেতাম আর একসঙ্গে ফিরতাম। গল্পগুজবে আর হাস্য পরিহাসে দু-মাইল রাস্তা কখন ফুরিয়ে যেত টেরও পেতাম না। বৈশাখের খররোদ আর আষাঢ়ের মুশলধারায় বৃষ্টি আমাদের কোনোদিন নিরানন্দ করতে পারেনি। চৈত্র মাসের বারুণি, স্নানের দিন থেকে আরম্ভ হত আমাদের মর্নিং স্কুল। সূর্য ওঠার অনেক আগেই রওনা দিতাম স্কুলে। শিশিরভেজা ঘাসের ওপর দিয়ে প্রাণ জুড়োনো ঝিরঝিরে শীতল হাওয়ায় খোলা মাঠের মধ্য দিয়ে দল বেঁধে স্কুলে যাওয়ার সে কী আনন্দ ভাষার মাপকাঠি দিয়ে তার গভীরতা নির্ণয় করা চলে না। মাঠজুড়ে সবুজের মেলার মধ্যে দেখতাম প্রকৃতির অবর্ণনীয় দৃশ্যসম্ভারের আয়োজন। স্কুল থেকে ফেরার পথে পরের গাছ থেকে ঢিল ছুঁড়ে আম পাড়ার প্রতিযোগিতা ছিল আমাদের নিত্যকার কাজ।
বর্ষায় চারিদিক যখন জলে জলময় হয়ে যেত তখন স্কুলে যেতে হত নৌকোয় করে। আমাদের ঘাটে বাঁধা নৌকোয় যেয়ে সবাই উঠতাম–প্রত্যেকের এক হাতে বই-খাতা, আর এক হাতে নিজ নিজ বইঠা। স্কুলের গায়ে নৌকো ভিড়িয়ে একই সঙ্গে ঝুপ ঝুপ করে বইঠা ফেলে উঠে যাওয়া, ফেরার পথে অন্য গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে বাইচ প্রতিযোগিতা, এসব কি সহজে ভোলবার! আমাদের গ্রাম থেকে অনেক দূরে বলরামপুরের নদী। ধান-পাট কাটা শেষ হওয়ার আগেই যাতে জল এসে সমস্ত ডুবিয়ে না দেয় সে জন্যে প্রতিবছরই নদীর মুখে তৈরি করা হয় প্রকান্ড একটা বাঁধ। জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি সময় থেকেই আমরা দিন গুনতাম কবে বাঁধ কেটে দেওয়া হবে আর কবে আমাদের পুকুরে জল পড়বে। পুকুরে বিপুল স্রোতে জল আসত। তা ছিল আমাদের একটা বড়ো আকর্ষণ। হঠাৎ একদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই হয়তো শুনতে পেতাম জলস্রোতের একটানা কল্লোল, বুঝতাম পুকুরে জল পড়ছে। তখন কোথায় থাকত ভোরবেলার সুখনিদ্রা, কোথায় থাকত পড়াশোনা–ছুটতে ছুটতে গিয়ে ডেকে নিয়ে আসতাম মাখন, রবি আর কেষ্টদের। মাছ ধরার হিড়িক পড়ে যেত। জেলেরা স্রোতের মুখে বড়ো বড়ো জাল পেতে ‘খরা’ তৈরি করত মাছের জন্যে। মাছ ধরার সে কৌশলটি একমাত্র পূর্ববাংলায়ই দেখেছি।
আমার গ্রামের চাষিদের কী সুন্দর সরল জীবনযাত্রা! ভোরবেলা যখন দেখতাম কাঁধে হাল আর কোঁচড়ে মুড়ি নিয়ে চাষির দল এগিয়ে চলেছে, তখন কতদিন মনে ইচ্ছে জাগত অমনি করে ওদের সঙ্গে মাঠে যেতে। মাঠেও আল ধরে কোথাও যেতে যেতে যখন দেখতাম নিড়ানি হাতে গান করতে করতে খেতের মধ্যে ওরা কাজ করে চলেছে–মন যেত তখন উন্মনা হয়ে আর নিজের অজ্ঞাতেই যেন পা দুটো দাঁড়িয়ে যেত। যেকোনো ঘটনাকে উপলক্ষ করে নিজেরাই মুখে মুখে ওরা রচনা করত গান–আর সেই গান তারা উন্মুক্ত প্রান্তরে দল বেঁধে গলা ছেড়ে গাইত প্রচন্ড রোদে চাষের কাজ করতে করতে। গ্রামের দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ মাঠের কথা মনে পড়লে আজও কানে বাজে সেই সুর। মনে হয় এখনও যেন সেই সুরেই ওরা গেয়ে চলেছে,
শুনেন সবে ভক্তিভাবে কাহিনি আমার–
শিবনাথপুরের কুমুদবাবু ছিলেন জমিদার,
ছিল সে ডাঙাদার,
ছিল সে ডাঙাদার, নাম তার ছিল জগৎজুড়ে,
জ্যৈষ্ঠ মাসের ১২ তারিখ ঘটনা মঙ্গলবারে।
মলো সে অপঘাতে,
মলো সে অপঘাতে, গেল সাথে দুনিয়ার বাহার–
তারপরে শুনেন বাবুর বাড়ির সমাচার।
বাবু যখন যাত্রা করে,
বাবু যখন যাত্রা করে গাড়িতে চড়ে রওনা
হতে যায়,
টিকটিকির কত বাধা পড়ে ডাইনে আর বাঁয়।
তা শুনে ঠাইগরানি কয়,
তা শুনে ঠাইগরানি কয়, বলি তোমায়
গঞ্জে যেয়ো না,
ঘটতে পারে আপদ বিপদ পথে দুর্ঘটনা।
স্বপ্নের কথা বুড়ি করিল বর্ণনা।
সব কথা অবশ্য আজ আর মনে নেই। বিপর্যস্ত জীবনযাত্রায় স্মৃতিও হয়ে আসছে ধূসর। তবু জানি আজও গ্রামের সাধারণ মানুষের দল তেমনি আত্মীয়তায় আমার কথা মনে রেখেছে। মনে রেখেছে আমায় সেই রশিদ, সওকতের দল। মনে রেখেছে আজিজুল, জেলহেজভাই। তবু নাকি সে গ্রাম আর আমার নয়। আমি আজ শরণার্থী।
.
ঘাটাবাড়ি
পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ থেকে মাইল আঠারো দূরে একটি সাধারণ ছোটো গ্রাম। ইতিহাসে খ্যাতি নেই। তবু গ্রামখানি স্বয়ংসম্পূর্ণ। নাম ঘাটাবাড়ি। এর পাশ দিয়েই বয়ে গেছে ছোট্ট নদী আঠারদা। কয়েক মাইল দূরে কান্ত কবি রজনীকান্ত সেনের জন্মস্থান ভাঙাবাড়ি। গ্রামের ইতিহাসে যার নাম অবিস্মরণীয় তিনি হলেন রাজা বসন্ত রায়। এই বসন্ত রায় কে? তাঁর আসল পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে তাঁর সম্বন্ধে এ অঞ্চলে জনশ্রুতির অভাব নেই। পাশের গ্রামে বসন্ত রায়ের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আজও পড়ে রয়েছে। তাঁর কালের বলে বর্ণিত বড়ো বড়ো দুটি জলাশয় ‘ধলপুকুর’ ও ‘আন্দ পুকুর’ (অন্দর পুকুর) স্বল্প জলের সম্বল নিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছে আজও।
বাংলার সত্যিকারের সৌন্দর্য তার প্রকৃতির লীলা বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায় উত্তর ও পূর্ববাংলায়। পল্লবঘন বৃক্ষরাজির ছায়ায় শান্তির নীড় এক-একটি গ্রাম। সেই লক্ষ গ্রামেরই একটি গ্রাম এই ঘাটাবাড়ি। গ্রীষ্মের শীর্ণ নদী সংকুচিত তীরভূমিতে ক্ষীণধারায় দিয়ে যায় তার স্নিগ্ধ শীতল পরশ। বর্ষায় ফিরে পায় তার হারানো যৌবন। নদীটির সঙ্গেও অনেক লোকপ্রসিদ্ধি জড়িয়ে আছে। ঠাকুরমার মুখে শুনেছি, ওই নদীর মাঝখানে আঠেরোটি বড়ো বড়ো গর্ত আছে। অনেক কাল আগে নদীতে নাকি সিন্দুক ভেসে উঠত। কেউ বলত ওর মধ্যে মোহর আছে আবার কেউ বলত বাসনপত্র।
আমাদের অঞ্চলটা পাটের এলাকা। এককালে সিরাজগঞ্জ অঞ্চলে নদীর ধারে ধারে সাহেবদের বড়ো বড়ো কুঠি ছিল। আজ সেইসবই যমুনার কুক্ষিগত। নদী কল্লোলে তার কোনো ইঙ্গিত আজ আর পাওয়া যায় না। আমাদের গ্রামাঞ্চলে নীলের চাষও হত। অনেক জায়গায় বিশেষ করে ওই কুঠিপাড়ায় নীলকুঠির ধ্বংসাবশেষও পাওয়া যায়।
ছুটিতে গ্রামে যেতাম বাইরে থেকে। পুরো একদিন হেঁটে পরের দিন প্রায় বারোটা একটার সময় গ্রামের স্টিমার ঘাট সোয়াকপুরে পৌঁছোতাম। ঘাটে আসবার আগেই স্টিমারের আর্তনাদ আমাদের সচকিত করে তুলত। পাড়ে ভেড়বার সঙ্গে সঙ্গে ঝড়ের বেগে ছুটে আসত কুলিরা। কিনারায় দন্ডায়মান নর-নারীর উৎসুক মুখের মাঝখানে দেখতাম আমাদের চিরপুরাতন কর্মচারীর হাসিমুখ। শেষের পথটুকু যেতে হত গোরুর গাড়িতে। সারি সারি মাল, যাত্রী বোঝাই ছোটো ছোটো গোরুর গাড়ি। যেন মহাপ্রস্থানের যাত্রী সব। এমানী ভাইয়ের গাড়ি তৈরি থাকত আমাদের জন্যে। ছইয়ের ভেতর না বসে সব সময়েই আমি এমানী ভাইয়ের পেছনে বসতাম। জীর্ণ গাড়ির চাকার একটানা ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ কেমন জানি মোহ সৃষ্টি করত মনে। রৌদ্ররুক্ষ ধূলিময় পথ। শীর্ণকায় গোরুগুলোর মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছে। চালকের উদ্যত লাঠি দেখে অনেক কষ্টে যেন এগগাবার চেষ্টা করছে। এমানী ভাই মাঝে মাঝে হাঁক দেয়- ‘ডানি-ই ক্যারে, গোরু নৌড় পারে না ক্যা?’ গ্রামের ভেতর আঁকা-বাঁকা যাত্রাপথ। এপাশে ওপাশের বাড়ি থেকে ভেসে আসছে ঢেঁকির ঢপ ঢপ শব্দ। শোলার বেড়ার ওপর দিয়ে কিষাণ বউদের উৎসুক কৌতূহলী দৃষ্টি। খেতে কর্মরত চাষিদের প্রশ্ন–গাড়ি যাবে কোনে? হায়, এ সবই অতীতের রোমন্থন মাত্র। কাপড়ের আড্ডা ইনাদপুর এলেই আমাদের গ্রামের কাছে আসা হল। সোজা সড়ক দূর থেকে আমার গ্রামকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। গোরুর গাড়ি থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটে আসতেন জসীম কাকা। আগেই বলেছি, গ্রামটি ছোটো হলেও স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাজার-হাট, ডাকঘর, স্কুল, খেলার মাঠ সব কিছুই সেখানে গ্রামের ধনী-দরিদ্রের সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আমাদের বাড়ির সামনেই ছিল ডাকঘর। দুপুরবেলায় দেখতাম গ্রামের পথ দিয়ে দেশ-বিদেশের সুখ-দুঃখের চিঠি ভরতি থলি ঝুলিয়ে এবং ঘণ্টাবাঁধা বল্লম কাঁধে নিয়ে ছুটে চলেছে রানার। তার ঠুন ঠুন শব্দ শুনে ছুটে আসত গ্রামের ছেলে-মেয়েরা। গ্রামের হাটটাও ছিল বাড়ির খুব কাছেই। ডাকঘরের সামনের ছোটো রাস্তাটি ধরে এগোলেই হাট। তার কিছু দূরে এম. ই. স্কুল। আমার পিতামহের প্রতিষ্ঠিত। আমার কাকা ছিলেন এর প্রধানশিক্ষক, সামনেই খেলার মাঠ। গ্রীষ্মের অপরাহ্নে গাঁয়ের তরুণদল সেখানে ফুটবল খেলায় মেতে উঠত। পাশ দিয়ে চলে গেছে ইউনিয়ন বোর্ডের অপ্রশস্ত সড়ক। বর্ষায় মাঠ, সড়ক সব ডুবে যেত। বর্ষাকালে গ্রামের চেহারা হয় অপূর্ব। শুধু জল, থইথই করা জল। নৌকো ছাড়া কোথাও যাওয়ার উপায় নেই।
ফুটবল খেলা নিয়ে গ্রামে খুব হইচই হত। নিজেদের শিল্ড খেলা ছাড়াও অন্যান্য গ্রামের প্রতিযোগিতার খেলায় খেলতে যাওয়া হত। বেশ মনে পড়ে মালিপাড়ার ফাইনাল খেলার কথা। আমাদের গ্রাম যখন তিন গোলে বেতিল গ্রামকে হারাল তখন হিন্দু-মুসলমান গ্রামবাসীর সে কী বিজয় উল্লাস!
বারোমাসে তেরো পার্বণের দেশ আমাদের। অন্যান্য পুজো-পার্বণ ছাড়াও চড়ক পুজো আমাদের গাঁয়ের উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। চৈত্র মাসে পাট-ঠাকুরের পুজো আরম্ভ হয়। পাট ঠাকুরের আসল ইতিহাস জানি না। তবে শুনেছি শিবপুজোরই এ এক ভিন্ন প্রথা। চৈত্র সন্ন্যাসীরা পাড়ায় পাড়ায় প্রত্যেক বাড়িতে পাট-ঠাকুর সামনে রেখে নাচ-গান করে। সংক্রান্তির দিন তাঁরা মিলিত হয়, খোলার কালীবাড়িতে। এখানে এ উপলক্ষ্যে বসে বড়ো মেলা। গ্রামের ছেলেবুড়োরা যোগ দেয় এই আনন্দ উৎসবে। সন্ধ্যায় দুজন হর-পার্বতী সেজে নাচে। তারপর আরম্ভ হয় চড়ক ঘোরানো। হিন্দুর অনুষ্ঠানে মুসলমানরা সানন্দে অংশগ্রহণ করত; আবার তাদের অনুষ্ঠানে হিন্দুরাও তেমনভাবেই যোগ দিত।
আমাদের বাড়ির পুবদিকে ঠাকুরবাড়ি। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে ওখানে হত কীর্তনগান। ঠাকুরমশাইরা একে একে সবাই গত হয়েছেন। তাঁদের ছেলে মেয়েরা অসহায় অবস্থায় পূর্ব বাংলার পরিস্থিতিতে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন। আজকের সন্ধ্যায় ঠাকুরবাড়িতে হয়তো আর খঞ্জনির ঝনঝনি শব্দ শোনা যায় না। শোনা যায় না সুমধুর শঙ্খধ্বনি বা কাঁসর ঘণ্টার বাজনা। গৃহিণীরা আজ আর কেউ হয়তো সেখানে গলায় আঁচল দিয়ে তুলসীতলায় সন্ধ্যাদীপ জ্বালে না। আমার গাঁয়ের এক-একটি তল্লাট জুড়ে আজ হয়তো দেখতে পাওয়া যাবে আমার মনের মতোই এক-একটি ফাঁকা মাঠ। কিন্তু হাসির ঝরনাধারায় আবার কি আমার গ্রাম সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে না?
হায় রে পৃথিবীর গতির বুঝি পরিবর্তন হয়েছে। তা না হলে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ধারা এমনভাবে সাম্প্রদায়িকতার মরুতে হারিয়ে যেতে পারে? দুঃখ-সুখের জোয়ার ভাটায় তারা যে একই সঙ্গে চলেছিল। আজ সেই শান্তির জীবনে অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে পড়েছে একদলের মনে সংশয় মৃত্যুভয়। নিজের জন্মভূমিতে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করবার অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। আজকের এই লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ সবহারাদের দল কি পথে প্রান্তরেই প্রাণ দেবে? শত সহস্র বীরের রক্তস্রোত কি ব্যর্থ হবে?
.
সাহজাদপুর
ঈশ্বরদী থেকে সিরাজগঞ্জ লাইনে ছোট্ট স্টেশন উল্লাপাড়া। স্টেশন ছোটো হলেও খুব কর্মব্যস্ত। মেল আর এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ। চালানি মাল, মাছ, পান, পাট–ওঠে নামে। বড়ো বড়ো ব্যাপারীর আনাগোনায় রেল স্টেশন উল্লাপাড়া সর্বদাই সজাগ।
স্টেশনের সিঁড়ি দিয়ে বাইরে নেমে গেলেই শুনতে পাবেন : ‘আয়েন বাবু আয়েন বলদ দেহেন দেহি আমার, যেন হাতিশালের হাতিছোটো যহন দেহেন যেন পঙ্খিরাজ ঘোড়া। এমনি একের পর এক গোরুর গাড়ির চালক এসে প্রলুব্ধ করবে আপনাকে। কেউ এসে বলবে : ‘ছইখান দেহেন দেহি। অট্টেলিকা বাবু, বজ্জর পলেও খাড়া, একখানি কাবারি নাহি খসে।’
‘যাবেন কনে, সাজাদপুর? গেরাদহ? চক্ষের নিমেষে লইয়া যামু।’
গোরুর গাড়ি ছাড়া খরার দিনে গতি নেই। যে গ্রামেই যান, মাইলের পর মাইল আপনাকে যেতেই হবে গোরুর গাড়িতে উল্লাপাড়া স্টেশন থেকে।
পথ আর ফুরোয় না। চলেছে তো চলেইছে। বিরক্তি প্রকাশ করলে মাঝে মাঝে গাড়োয়ান তাড়া দেয় বলদ দুটোকে ল্যাজ মলে। অমনি কিছুদূর পর্যন্ত বেশ জোরে ছুটে চলে গাড়ি। দু হাত দিয়ে তখন ছইয়ের বাঁশ চেপে ধরতে হয়–ভয় হয়, গাড়ি উলটে নীচে পাশের ধানখেতে পড়ে গেলে আর রক্ষে নেই। তবে ভাবতে ভাবতেই ভয় কেটে যায়। গাড়ির গতি আবার মন্থর হয়ে আসে। উচ্চৈ:স্বরে গাড়োয়ান গেয়ে ওঠে পুরোনো একটা গান : ‘দরদি রে, তোর ভাঙা নৌকায়…।’ নানা সুরের দোল খেতে খেতে গানের প্রথম কলিটিই মাঝপথে থেমে যায়–শেষ আর হয় না। বাঁয়ের বলদটার পেটে পা দিয়ে ঠেলা দিয়ে গাড়োয়ান বলে ওঠে–দ্যাখ দিনি, ডাঁয়ে ডাঁয়ে…।
ছোটো ছোটো গ্রাম পার হতে হয় একে একে। বেতবনের আর বাঁশবনের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে টিনের চাল আর খোড়ো ছাউনির আগল চোখে পড়ে এখানে-ওখানে। উৎসুক হয়ে গ্রামের মেয়ে-বউয়েরা মুখ বার করে দেখে আর একজন আর একজনকে জিজ্ঞেস করে–কোন গাঁয়ে যায় রে?
গাড়োয়ান সবারই পরিচিত। হেঁকে বলে– সাজাদপুর, সাজাদপুর। কোমরে কাপড় জড়ানো, ছোটো ঘোমটায় আঁটসাট মুখগুলো মনে হয় আপন, বড়ো নিজের–যেন স্নেহ মমতায় ভরা নিজের ঘরের মা আর বোন। ইচ্ছে করে নেমে গিয়ে শুধোই। কত সুখ, কত পরিতৃপ্তির পরিবেশে ঘর বেঁধে আছ তোমরা, শোনাবে তোমাদের গল্প, বলবে তোমাদের কথা?
ঢিবি পার হয়ে ঘচাং করে নীচে নেমে আসে ওই পঙ্খিরাজদের গাড়ি আর পেছনে ফেলে যাই এমনি করে গ্রামের পর গ্রাম। তারপরেই দু-দিকে ধু-ধু মাঠ। মাঝে মাঝে শুধু টেলিগ্রাফের পোস্ট, তারা যেন বলছে–এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও, আরও আছে পথ।
একবার গভীর রাতের গাড়ি থেকে নেমে চলেছিলাম এমনই এক গোরুর গাড়িতে। পথ অনেক, তাই গাড়োয়ান পোয়ালের ওপর বিছানা খুলে দিয়ে ছইয়ের খোলা মুখ দুটোয় কম্বলের পরদা টাঙিয়ে দিয়ে বলল–ঘুমায়ে পড়েন বাবু, শীতের রাত। যাবেন ধীরে ধীরে।
মাথায়-কানে গামছা জড়িয়ে ফয়েজ আলি গাড়ি চালায়। বেশ আরামে চলেছি–চোখ দুটোও বোধহয় ধরে এসেছে। চমক ভেঙে গেল ফয়েজের গানে,
আমায় শুধস নারে, কোন গাঁয়ে যাই–
ও সে, কালো চক্ষের জল দেখেছি
ফুলের নূপুর পায়।
তার দিঘল চোখের কাজল
আমার অঙ্গে লাগে নাই রে…
ও ভাই শুধস নারে…
কী দরদটালা গলায় ফয়েজ গেয়ে চলেছে! নিস্তব্ধ রাত–ফিকে জোছনা, ফাঁকা মাঠের হাওয়ায় বার বার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে : আমায় শুধস নারে…। ওদের মেঠোসুরে গলার বাঁধুনি এত সুন্দর লাগে কেন? কে ওদের শেখায় এমন করে প্রাণঢালা গান গাইতে? আর একবার ফিরতি পথে গাড়োয়ান জমিরকে বলেছিলাম : জমির মিয়া, জানো ভাই ওই গানটা–সেই ‘তার দিঘল চোখের কাজল আমার অঙ্গে লাগে নাই রে? সে গাইল। একেবারে ভিন্ন সুর। কিন্তু তেমন করেই চঞ্চল করল আমার মন প্রাণ।
এই পথেই, ঠিক এই সব ঝোঁপঝাড় ধুলোবালির পথ পেরিয়েই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সাহজাদপুরের কুঠিবাড়িতে, ঠাকুর কাছারিতে গেছেন কতবার? এই কথা মনে হত বার বার উল্লাপাড়া থেকে আমার জন্মগ্রাম সাহজাদপুরে যেতে যেতে। প্রতিটি বট আর কুলের গাছ, প্রতিটি টেলিগ্রাফের পোস্ট দেখে মনে হত কবি হয়তো কখনো এদের কানে-কানে কোনো বার্তা দিয়ে গেছেন অনাগত পথিকের জন্যে! কবি এখানে আসতেন কখনো পালকিতে, কখনো বা গয়নার নৌকোয়। এই কুঠিবাড়িতেই ওপরতলায় বসে তিনি লিখেছিলেন, ‘পোস্টমাস্টার।
এই ঠাকুর-কাছারিতে কোনো এক টিনের চালার পাটকাঠির বেড়া-ঘরে কয়েকবার আশ্রয় পেয়েছিলাম। ঘুরে ঘুরে দেখতাম সেই বাঁধানো বকুলতলা, কুঠিবাড়ির গা-ঘেঁসে বড়ো বড়ো গয়নার নৌকোয় আনাগোনাবাজার-হাট ঘাট-মাঠ-পথ, আর ওই বিখ্যাত কাঠের পুলটা, যার মুখ গিয়ে ঠেকেছে পাটগুদামের মস্ত টিনচালার ঘরটার গোড়ায়। কত রাত অবধি আমরা দল বেঁধে কাটিয়েছি ওই কাঠের সাঁকোটার ওপর দাঁড়িয়ে। ভারি আনন্দ হত যখন তার নীচ দিয়ে একের পর এক নৌকো চলে যেত। কোনোটায় বোঝাই থাকত বাঁশ, কোনোটায় তামাক, কোনোটায় দুধ। জোয়ান মাঝিদের শক্ত হাতের লগি ঠেলায় সাঁৎ সাঁৎ করে বড়ো বড়ো নৌকোগুলো জলের বুকে মুখ রেখে পিছলে পিছলে এগিয়ে যেত। এক একদিন কুঠিবাড়ির লাইব্রেরির বারান্দায় বসে বসেই রাত প্রায় কাবার করে দিতাম। মুরগি ডেকে উঠত ওপারে চাষিদের উঠোনে। তখন বাড়ি ফিরতাম।
হাটে-বাজারে সর্বত্রই প্রায় বেড়ার ঘর। পাটকাঠির বেড়া, হেঁচা বেড়া, অথবা খলপার বেড়াই বেশি। ওপরে টিনের চাল। কোথাও-বা বেড়ার গায়ে সুন্দর করে মাটি লেপা। পাকা দালানঘরও আছে অনেক।
ঠাকুর কাছারির সব কর্মচারীই একটি এলাকায় বাস করেন–ম্যানেজার সাহেব থেকে দপ্তরি পেয়াদা অবধি সকলেই। কাছারির তরফ থেকে বাসা দেওয়া হয় সবাইকে।
অপর্যাপ্ত দুধ আর মাছের বাজার সেখানে। ইলিশমাছ আর দুধ যে অত সস্তা হতে পারে তা ভাবাও যায় না। লোকে বাজারে দুধ আনতে গেলে বালতি নিয়ে যেত সঙ্গে করে। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দেও এরকম সচ্ছল অবস্থা ছিল সেখানে।
বর্ষাকালে (দুর্গাপুজোর আগে অবধি) নৌকো ছাড়া যাতায়াতের উপায় থাকত না। চরিদিকে থইথই জল। গভীর রাতে বাঁশ আর বেতবনের ভেতর দিয়ে ছপ ছপ শব্দে বৈঠা ঠেলে ঠেলে ছোটো-বড়ো নৌকোগুলো যেত-আসত। হাটের দিনে সেই যাতায়াত প্রায় সারারাতই লেগে থাকত। নৌকোর ওপরই রান্না করছে মাঝিরা, সেইখান থেকেই হাঁড়ি-বাসন ধুয়ে নিচ্ছে, সেইখানেই আহার সারছে। জলেই যেন ওদের ঘরকন্না। একবার একটানা পাঁচ দিন রইলাম এই নৌকার ঘরে। পাবনা জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতাম। কত বিচিত্র পথে আনাগোনা–তার শেষ নেই। হ্যারিকেন লণ্ঠন নৌকোর মাথায় তুলে দিয়ে ছইয়ের ওপর উঠে বসে রাত্রের অন্ধকারে মাইলের পর মাইল যাও–চারিদিকে জলরাশি–কোথাও-বা উঁচু–কোথাও নীচু। যেসব হাঁটাপথে একবার হেঁটে গেছি তারই বুকের ওপর দিয়ে জলরাশি ভেদ করে নৌকোয় যেতে সে কী আনন্দ! নিশুতি রাত। তবু বহুদূরের নৌকোর ডাক স্পষ্ট শোনা যায়। আর বহুক্ষণ ধরে তার মাথায় টিমটিম আলো দেখা যায়। সহযাত্রী জোটে। দুই নৌকো পাশাপাশি চলে। তীরের ওপর দিয়ে দুজন হয়তো বা গুণ ধরে চলে। জলের ভেতর পা দুটো ডুবিয়ে বসে শুনি ওদের গলাছাড়া গান,
ও কালা শশী রে
আর বাজায়ো না বাঁশি–
বাঁশি শুনিতে আসি নাই আমি,
জল নিতে আসি…।
গলার অত জোর, অথচ মিষ্টত্ব নষ্ট হয় না–প্রাণঢালা দরদ মেশানো গান।
বড়ো বড়ো গয়নার নৌকো জোড়া জোড়া ঢাক পিটিয়ে চলে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। আট, দশ, পনেরো কুড়ি মাইল–একটানা পথ। ঢাকের গগনভেদী শব্দে জানা যায়-গয়নার নৌকো চলেছে। ভেতরে শুয়ে বসে বহুযাত্রী একসঙ্গে যেতে পারে। কী শক্ত গড়ন–যেন লোহার তৈরি এই নাও।
দুর্গাপুজোর মতোই সরস্বতীপুজো এইদিকে মহাসমারহে হত। সেই সময় বসত গানের আসর-দূর-দূরান্তর থেকে আসতেন নানা গুণীজন। সাহিত্যসভায় বাংলাদেশের স্বনামধন্য অনেকেই আসতেন। যেবার অনুরূপা দেবী সভানেত্রী সেবার আমি ছিলাম উপস্থিত। নাচ, গান, কবিতা প্রতিযোগিতা লেগে থাকত তখন প্রায় প্রত্যেকটি সন্ধ্যায়।
পাবনা জেলার সাহজাদপুর, জামিরতা, পরজনা, বাঘাবাড়ি–এদের আর-এক রূপ দেখেছি পঞ্চাশের মহামন্বন্তরে। কোথায় ছিল এত লোক? এই নরকঙ্কালের দল? একটু ফ্যানের জন্যে ঘুরে বেড়াত ওরা বেড়ার গায়ে গায়ে। যে বাড়িতে ছিলাম, সেই বাড়িতে রাত্রে রান্নাঘরে ধরা পড়ল একটি চৌদ্দ-পনেরো বছরের ছেলে। অনেক লোকজন চোর মনে করে লাঠি-সোঁটা নিয়ে ছুটে এল–ভাতের হাঁড়ি থেকে দুই হাতে ভাত তুলে মুখে দিচ্ছে ছেলেটা–এতটুকু ভয় বা উদবেগ যেন তার নেই।
যেসব মাঠে সোনার ফসল ফলেছে একদিন সেই ধানখেতেই বহু নরকঙ্কাল পড়ে থাকতে দেখেছি এখানে-ওখানে। চোখের সামনে খিদের জ্বালায় মানুষকে মরতে দেখেও মানুষ নিজের অন্নের ভাগটুকু সামলে রেখেছে। আগে যাকে দেখেছি ঘরের বউ, সন্তানের মা, পচা ময়লা ঘেঁটে খাদ্যের সন্ধানে তাদেরও ঘুরে বেড়াতে দেখলাম। পরিচয় থাকা সত্ত্বেও কথা বলেনি তারা–শুধু জ্বলন্ত চোখ তুলে একদৃষ্টে চেয়ে থেকেছে। বেশিক্ষণ সে-দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে সাক্ষাৎ ভগবানও বুঝি ভয় পাবেন!
কাছারি বাড়ির ওপারেই কামারের ঘর। দিনভর ভারী হাতুড়ির ঠোকাঠুকি লেগেই আছে। কখনো গোরুর গাড়ির চাকায় লোহার বেড় লাগানো, কখনো কোদাল-কুড়ল-দা-খোন্তা তৈরি হচ্ছে। কামার বলে ঠাউর, আইচেন কন থিয়্যা?
শুনি ওদের কাজকর্মের কথা।
বিখ্যাত ছিল সূর্য রায়ের হোটেল। পাবনা জেলার গেজেট বলা হত ওকে। গ্রাম-গ্রামান্তরের খবর পাওয়া যেত সেখানে গেলে। কত জায়াগার লোক এসে জোটে। সন্ধের পর প্রত্যহ জমে মজলিশ–গল্পের, তাসের আর দাবার। হাটবাজার বন্ধ হয়ে গেলে সূর্য রায়ের হোটেল জমে ওঠে।…
আজও হয়তো সেই আড্ডা জমে, গয়না নৌকোর ভিড় জমে নদীতে, গাড়োয়ান সেইরকম উদাত্ত গলায় গান গেয়ে যায়, শুধু আমরা আর সে আড্ডায় যোগ দিতে পারি না, সেই গান শুনতে পাই না। র্যাডক্লিফের কুড়লের ঘায়ে সাহজাদপুর যে আজ আলাদা হয়ে গেছে! মায়ের সঙ্গে ছিঁড়ে গেছে আমার যোগ।
ফরিদপুর জেলা – কোটালিপাড়া রামভদ্রপুর কাইচাল খালিয়া চৌদ্দরশি খাসকান্দি কুলপদ্দি
বিশাল বনস্পতিও ধরাশায়ী হয় প্রচন্ড ঝোড়ো হাওয়ায়, বুনো হাতির পায়ের চাপে সাজানো ফুলের বাগান যায় বিপর্যস্ত হয়ে। ঠিক তেমনি তো হয়েছে আমার পুববাংলার হাজার হাজার সোনার পল্লি-প্রতিমার অবস্থা–জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে গেছে গ্রামের পর গ্রাম ভুল রাজনীতির আকস্মিক অশনিপাতে। বহুপুরুষের যত্নে গড়া কত বাড়িঘর আজ পড়ে আছে শ্রীহীন হয়ে, খাঁ খাঁ করছে কত বিদ্যায়তন, কত দেউল। শিবশূন্য শিবালয়গুলোতে হয়তো চলেছে অশিবের হানাহানি, হয়তো বা অনেক মঠ-মন্দির লুপ্তও হয়ে গেছে এত দিনে। আর ভারতবর্ষের ইতিহাসে এ তো নতুন কিছু নয়–দেবালয় ধ্বংসের অভিযান অনেকবারই প্রত্যক্ষ করতে হয়েছে ভারতবাসীকে।
একটা ক্রুদ্ধ রুদ্র নিশ্বাসে সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রবহমান ধারা যেন হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে পুববাংলায়। অতীত ইতিহাসের কত গৌরবময় স্মৃতি জড়িয়ে আছে বাংলার এক-একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে; কিন্তু আজ যেন এক একটা ছেড়ে আসা গ্রামের অধিবাসীদের সঙ্গে সঙ্গে পল্লিমায়ের সেই সব স্মৃতির আভরণ ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে দিগবিদিকে। এমনি এক গ্রাম-মায়ের কোল থেকেই প্রথম সূর্য-প্রণাম করেছিলাম আমি প্রায় বছর চল্লিশ আগে। আজন্ম আত্মীয় সে মাটি আজ আমার পর–এ সত্য, না স্বপ্ন! সত্য হলেও গ্রামকে নিয়ে গর্বের যে অন্ত নেই।
আমার জন্মভূমি কোটালিপাড়া শুধু গ্রাম নয়, আবার পরগনাও। বাংলার এককালীন বিদ্যাপীঠ নবদ্বীপ সম্বন্ধে যেমন বলা হত-নবদ্বীপে নবদ্বীপ গ্রাম, পৃথক পৃথক কিন্তু হয় এক নাম’, এও অনেকটা তাই। পাশাপাশি কাজোলিয়া, মাজবাড়ি, পশ্চিমপাড়া, ডহরপাড়া, পিঞ্জুরি, ঊনশিয়া, মদনপাড়, দিঘির পাড়, রতাল এবং এমনি আরও বহু জনপদের সমষ্টিগত গ্রাম-নাম কোটালিপাড়া। এসব জনপদের লোকেরা বাইরে গিয়ে চিরকালই নিজেদের পরিচয় দিয়ে আসছে কোটালিপাড়ার অধিবাসী বলে। গোপালগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত এই পরগনা গ্রামের মাঝখান দিয়ে বয়ে গেছে পুণ্যতোয়া ঘাগর নদ। ছোটোবেলা থেকেই দেখে এসেছি প্রতিবছর চৈত্র সংক্রান্তির দিনে লক্ষ লক্ষ লোককে এর শীতল জলে স্নান করে গঙ্গাস্নানের পুণ্যার্জন করতে। সে উপলক্ষ্যে এর তীর জুড়ে বসত বিরাট মেলা। আজও কি বসে সেই মেলা? মেলার উল্লাসে মেতে ওঠার মতো মানুষের মন কি আজও আছে কোটালিপাড়ায়? আমার মন যে তা বিশ্বাসই করতে চায় না। ঘাগরেরই কোলে গড়ে উঠেছিল ঘাগর বন্দর। সে বন্দরের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল চারিদিকে। দেশের মাটিকে বিদায় দিয়ে আসার আগেও দেখে এসেছি কত দূর-দূরান্তরের কত পণ্যবাহী নৌকার ছড়াছড়ি সে বন্দরে! সেদিন এক বন্ধু এসে জানাল, ঘাগর বন্দরের যৌবনোচ্ছাস আর নেই, বার্ধক্যের ঝিমুনি লক্ষ করে এসেছে সে তার চোখে।
মনে পড়ে ঝনঝনিয়া, দেওপুরা, বরুয়া এবং বাগিয়া বিলের কথা। বিশাল জলরাশি বুকে ধরে এসব বিল এ অঞ্চলের মাটিকেই শুধু রসসিক্ত করেনি, এ পরগনার মানুষের মনেও বইয়ে দিয়েছে রসের বন্যা। কত গায়ক, বাদক, কথক এবং আরও কত জ্ঞানী-গুণী জন্মগ্রহণ করেছেন এ মাটিকে ধন্য করে। এই কোটালিপাড়ায় ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের কথা প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হয়েছিল। ‘বারোশো বামুনের তেরোশো আড়া, তার নাম কাশ্যপপাড়া’–-একটি অংশের পরিচয় থেকেই বাকি কোটালিপাড়া সম্বন্ধেও মোটামুটি একটা ধারণা মিলবে। কারণ প্রায় সব কোটালিপাড়া জুড়েই রয়েছে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের বাস। লক্ষাধিক লোকের বাসভূমি এ পরগনায় লক্ষ শিবের পুজো হত বলে কাশীতুল্য স্থান হিসেবে এর ছিল ব্যাপক প্রসিদ্ধি। নবদ্বীপ, বিক্রমপুর, ভাটপাড়া–বাংলার ব্রাহ্মণ্যবিদ্যার এই মুকুটমণিদলের মধ্যে কারও চেয়ে ন্যূন নয় আমাদের কোটালিপাড়ার স্থান।
এ অঞ্চলে এক-একটি দেবস্থান গড়ে উঠেছে এক-একটি গ্রামের কেন্দ্র-পীঠরূপে। সিদ্ধান্তের খোলার বহুবিশ্রুত চড়কপুজোর কাহিনি যে কত পুরোনো তা জানা নেই। অনেক অলৌকিক স্মৃতি জড়িয়ে আছে এই চড়কপুজোর সঙ্গে। ভয়ে ও শ্রদ্ধায় এ এলাকার মুসলমানেরাও চড়কঠাকুরকে প্রণামি দিয়ে আশীর্বাদ ভিক্ষা করে আসছে চিরকাল। হরিণাহাটি ও পশ্চিমপাড়ার কালীবাড়ির সঙ্গেও জড়িয়ে আছে অনেক পুরোনো কথা। মদনপাড়ের গোবিন্দের, সিদ্ধান্তবাড়ির বুড়ো ঠাকুর, রতালের মনসাদেবী, সিদ্ধেশ্বরী মাতা ও লক্ষ্মী নারায়ণের বিগ্রহও সমধিক প্রসিদ্ধ।
একেবারে ছোটেবেলা থেকেই রতালের মনসাদেবী সম্বন্ধে কত গল্প শুনে আসছি। জনপ্রিয় দেব-দেবীর মধ্যে বাংলাদেশে মনসাদেবী নাকি একেবারে জাগ্রত। রঘু গাইনের নাম আজও কোটালিপাড়ার লোকের মুখে মুখে। এক সময় ফরিদপুরে সর্বত্র মনসার গান গেয়ে বেড়াতেন ইনি সদলবলে। সে প্রায় শ-দুই বছর আগেকার কথা। প্রত্যাদেশে মনসা পেয়ে যে দেবীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রঘু গাইন তাই আজ রতালের মনসাদেবী নামে খ্যাত। আদিষ্ট গীতাবলি অবলম্বনেই মনসার গান গাইতেন রঘু গাইন। অনেক অভূতপূর্ব ঘটনার কথা প্রচলিত আছে এই দেবী ও তাঁর ভক্ত রঘু গাইন সম্বন্ধে। ১৩২৬ খ্রিস্টাব্দে আশ্বিনের ঝড়ে রতালের গাইন বাড়ির সব ঘর ধুলিসাৎ হলেও যে ঘরে মনসার চামর ছিল সে ঘরখানি ঠিক দাঁড়িয়েই ছিল। আশ্চর্য ঘটনা বই কী। কিন্তু আজ যে সেই মনসাদেবীর চামর নিয়েই রঘু গাইনের বংশধরগণকে গ্রাম ছেড়ে কলকাতা প্রবাসী হতে হল, অদৃষ্টের পরিহাস ছাড়া তাকে আর কী বলব? রঘু গাইনের প্রপৌত্র, রমাকান্ত গাইনের সময়ে এক রাত্রিতে নাকি ডাকাত পড়েছিল তাঁদের বাড়িতে। কিন্তু মনসাদেবী যে বাড়ীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী ডাকাতের ক্ষমতা কী যে সে বাড়ির কোনো ক্ষতি করবে? নাগকুল নাকি এমনি ভাবে ঘিরে রেখেছিল বাড়ির চারদিকের সীমানা যে, দস্যুদল সাপের ‘ফোঁস ফোঁস’ শব্দে বাড়ির ভেতর ঢুকতেই আর সাহস পায়নি। এ অনেককাল আগেকার কথা। রঘু গাইনের মনসাভক্তি সম্বন্ধে ছোটোবেলায় একটি অদ্ভুত কাহিনি শুনেছিলাম। সেই অলৌকিক ঘটনার কথা আজও মনে পড়ছে। ফরিদপুর জেলার বাইটামারি গ্রামে কোনো এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাড়িতে এক নবজাতকের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে হয়েছে মনসা পুজো। মনসা ভাসানের গান গাইবার জন্যে আমন্ত্রণ হয়েছে দুটি বিখ্যাত দলের। তার মধ্যে একটি হল রঘু গাইনের দল। গাইনের দল আসতে একটু দেরি করে ফেলায় ধনী গৃহস্থামী এতটা উত্তেজিত হয়ে গেলেন যে, তাঁদের গানের আর প্রয়োজন নেই বলেই জানিয়ে দিলেন তিনি। আর কোনো উপায় না দেখে, ফিরে যাওয়ার আগে মনসাদেবীকে একবার প্রণাম জানিয়ে যেতে চাইলেন রঘু গাইন। প্রার্থনা মঞ্জুর হল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ নির্দেশও দেওয়া হল যে, কৃত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তাঁকে পশ্চার্দিক থেকে দেবীকে প্রণাম করতে হবে- আসরে ঢুকে সম্মুখ থেকে তাঁকে প্রণামের অধিকার দেওয়া হবে না। তাতেই রাজি হলেন রঘু। মন্ডপের পেছনে গিয়ে গানের সুরে প্রণাম জানালেন তিনি দেবীকে। অপূর্ব তন্ময়তা সে গানে। সমবেত জনতা যখন সে সুরের মূর্ঘনায় বিভোর সেই অবকাশে কখন যে দেবী প্রতিমা ঘুরে গেছে পেছন দিকে কেউ তা লক্ষই করেনি। যখন চোখে পড়ল, তখন সে কী শোরগোল! শেষপর্যন্ত উলটো দিকেই দেবীর সামনে নতুন করে আসর বসিয়ে রঘু গাইনের মনসা ভাসানের গান শুনতে হল সবাইকে! কঠোর বাস্তবের আঘাতে বিপর্যন্ত আজকের বাঙালি দেব-দেবীর এসব অলৌকিক কাহিনি কী করে বিশ্বাস করবে?
তালতলা ভজন কুটিরের হরিসভার কথা মনে পড়ে। প্রতি পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাশুভ্র সন্ধ্যায় বসত সেখানে ভাগবতপাঠের আসর। ভক্তিযুক্ত মন নিয়ে কত পল্লিবাসী নর-নারী আসত সেখানে কৃষ্ণ-কথা শুনতে, আমিও যেতাম। সিদ্ধেশ্বরী মাতার মন্দিরেও দেখেছি অজস্র লোক সমাগম হত বার্ষিক উৎসবে, শিবচতুর্দশী ও কালীপুজো উপলক্ষ্যে। রতালের মহাশক্তি আশ্রমে লোকেদের ভিড় লেগেই থাকত। আমাধ্যক্ষ আচার্য বরদাকান্ত বাচস্পতি জ্যোতিষ ও তন্ত্রশাস্ত্রে সুপন্ডিত। এঁর জ্যোতির্বিদ্যায় মুগ্ধ হয়ে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে সবাই এসে আপদে বিপদে জড়ো হত সেখানে। বাস্তবিকপক্ষে মহাশক্তি আশ্রম কোটালিপাড়ায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলনক্ষেত্র। শুধু বাংলা দেশের নয়, ভারতের দূরান্তবর্তী অঞ্চল থেকেও অনেক লোককে আসতে দেখেছি এ আশ্রমে জ্যোতিষী মাহাত্মের ফলোভের জন্যে। বাচস্পতি মশায়ের গণনা সম্বন্ধে কত যে অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প রয়েছে তারও শেষ নেই। শুধু গণনাকার্যের জন্যেই নয়, ভজনকীর্তনে, কাঙালি ভোজনে, অতিথিসেবায় সর্বদাই থাকত এ আশ্রম মুখরিত। রতালের মনসাবাড়ি নামেও খ্যাত ছিল এ বাড়ি। আশ্রমমাতা জ্ঞানদাদেবী প্রসাদবিতরণে, দরিদ্রনারায়ণসেবায় ছিলেন অন্নপূর্ণারূপিণী। পঞ্চাশের মন্বন্তরে কত হিন্দু মুসলমানের যে প্রাণরক্ষা হয়েছে এই আশ্রমমাতার কৃপায় গ্রামবাসীরা কি সে-কথা ভুলতে পারে! কিন্তু তবু এঁদের সবাইকে চলে আসতে হয়েছে প্রিয় গ্রাম ছেড়ে। শুনেছি সেই মহাশক্তি আশ্রম উঠে এসেছে কলকাতা পাইকপাড়ায়। সেখানে নাকি লোকের ভিড়ের অন্ত নেই, শ্রীশ্রীনারায়ণ ঠাকুরের দর্শনার্থী সেখানে আসে দলে দলে। কিন্তু কোটালিপাড়ার সেই পরিবেশ পাওয়া কি সম্ভব কলকাতায়? আমার গাঁয়ের হরিসভায় আর ভাগবতপাঠের আসর বসে না, সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে আর হয় না উৎসব আয়োজন!
কত মহাজ্ঞানী ও গুণীজনের আবির্ভাবে ধন্য আমার কোটালিপাড়া। আবার কি আমরা ফিরে যেতে পারব না সেখানে? পথহারা হয়েও পথ চলতে চলতে তার আকুল আহ্বান সব সময়ই তো শুনতে পাই, কিন্তু তার ডাক শুনেও পা এগোতে চায় না কেন সেদিকে? আজও কি পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হয়নি আমাদের পাপের? আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাই কোটালিপাড়ার অতীতকে স্মরণ করে। বেদান্ত শাস্ত্রে আচার্য শঙ্করতুল্য মহাপন্ডিত স্বর্গীয় মধুসূদন সরস্বতী জন্মপূত ঊনশিয়া কোটালিপাড়ারই অন্তর্গত। মধুসূদনের পান্ডিত্যের তুলনা বিরল। তাই তো কাশীর পন্ডিতসমাজে আজও প্রচলিত প্রশস্তিবচনে বলা হয়েছে তাঁর সম্বন্ধে,
মধুসূদন সরস্বত্যা পারং বেত্তি সরস্বতী।
পারং বেত্তি সরস্বত্যা মধুসূদন সরস্বতী।।
মধুসূদন সরস্বতীর বিদ্যার পরিমাণ স্থির করা একমাত্র দেবী সরস্বতীর পক্ষেই সম্ভব এবং একমাত্র মধুসূদন সরস্বতীই দেবী সরস্বতীর জ্ঞানপরিধির পারংগম। বিদ্যাদায়িনী সরস্বতীর সঙ্গে যার তুলনা করেছেন কাশীর পন্ডিতসমাজ তাঁর জন্মস্থানের লোক আমরা আজ গ্রাম মায়ের কোলছাড়া হয়ে অজ্ঞান অববাধের মতো ঘুরে বেড়াই চরম অসহায়তায়। মধুসূদন রচিত ‘অদ্বৈতসিদ্ধি’ অদ্বৈত বেদান্তের প্রামাণিক গ্রন্থরূপে ভারতের সর্বত্র প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। এবং ভারতের বাইরেও রয়েছে মধুসূদনের গুণমুগ্ধ বহু দার্শনিক পন্ডিত। নবদ্বীপ পাকা টোলের প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক ও পরে কাশীরাজের বৃত্তিভোগী কাশীবাসী প্রসিদ্ধ বৈদান্তিক ও নৈয়ায়িক স্বর্গীয় জয়নারায়ণ তর্করত্ন, জয়পুর রাজ কলেজের প্রাক্তন ন্যায়াধ্যাপক স্বর্গত কালীকুমার তর্কতীর্থ প্রমুখ পন্ডিতেরাও ছিলেন ঊনশিয়ারই অধিবাসী। বাস্তবিকপক্ষে কোটালিপাড়ার প্রধান গৌরব পন্ডিতস্থান হিসেবেই। এ অঞ্চলের পন্ডিতদের মধ্যে আজও যাঁরা জীবিত রয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে ব্যাসকল্প মহাপন্ডিত মহামহোপাধ্যায় ভারতাচার্য হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের কথা। ইনি আজ স্থানান্তরে একক সাধনায় মহাকায় মহাভারত রচনায় নিমগ্ন। পশ্চিমপাড়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন কোটালিপাড়ার প্রথম মহামহোপাধ্যায় পরলোকগত রামনাথ সিদ্ধান্ত পঞ্চানন ও প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক স্বর্গীয় শশীকুমার শিরোরত্ন। প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ স্বৰ্গত রাধারমণ রায় এবং বর্তমান যুগের ভারতখ্যাত অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুরশিল্পী তারাপদ চক্রবর্তীও (নাকুবাবু) এ গ্রামেরই ছেলে। আধুনিক শিক্ষায় সুপন্ডিত রাজনীতিবিদ ডা. ধীরেন্দ্রনাথ সেনের বাড়ি ছিল দিঘির পাড়ে এবং প্রখ্যাত সাংবাদিক চপলাকান্ত ভট্টাচার্যের গ্রামও কোটালিপাড়ারই মদনপাড়। বাঙালি শিল্পপতিদের অন্যতম স্বৰ্গত কর্মবীর সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য জন্মেছিলেন হরিণহাটিতে। কোটালিপাড়াকে বড়ো করার, সমৃদ্ধ করার কত পরিকল্পনা ছিল তাঁর! রতালে জন্মেছিলেন সুপন্ডিত ও সুগায়ক-কথক রঘুমণি বিদ্যাভূষণ এবং জ্যোতির্বিদ গোপাল মিশ্র। তাঁরা উভয়েই দেহরক্ষা করেছেন দীর্ঘকাল আগেই কিন্তু তাঁদের দেহই শুধু নয়, তাঁদের কীর্তিধন্য নামও যে জড়িয়ে আছে আমার গাঁয়ের সোনার মাটির সঙ্গে!
সমগ্রভাবে ব্রাহ্মণপ্রধান হলেও কোটালিপাড়ার কাসাতলী, গোয়ালঙ্ক, পিঞ্জুরী প্রভৃতি কয়েকটি জনপদ বৈদ্যপ্রধান এবং আধুনিক শিক্ষায় ও প্রগতির ক্ষেত্রে এঁরা অগ্রণী।
সাত সাতটি হাট, দুটো দৈনিক বাজার, চারটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়, দুটো সংস্কৃত কলেজ, দশ-বারোটি টোল, এবং তার ওপর থানা, ডাকঘর, সাবরেজেস্টারি অফিসে সবসময় জমজমাট থাকত আমার সাধের কোটালিপাড়া। আর আজ? এখন নাকি সরকারি অফিস ছাড়া একটি বাজার, দুটি হাট ও একটি উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় কোনোরকমে অতীত গৌরবের সাক্ষ্য বহন করছে বিদির্ণ কঙ্কালের মতো। সংস্কৃত শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে ছিল যার আসল পরিচয় সেখানে আজ একটিও টোল নেই, একজনও অধ্যাপক নেই–কোটালিপাড়ার মানুষ আমরা ভাবতেও যে পারি না সে-কথা!
আজ কত স্মৃতি জাগে মনে। বড়ো বড়ো পুজোপার্বণের কথা নাই বা বললাম! আমার গাঁয়ের মেয়েরা-মায়েরা মিলে বছরের পর বছর মঙ্গলচন্ডীর ব্রত করেছে সারাবৈশাখ মাস ধরে –প্রতিমঙ্গলবারে। তাঁদের সমস্ত মঙ্গলকামনার প্রতিদানে ঘোর অমঙ্গলের অন্ধকারে কেন আমাদের ঠেলে দিলেন মা মঙ্গলচন্ডী? তবে এই চরম অঙ্গলকে অতিক্রম করেই পরমমঙ্গলের সন্ধান পাব আমরা? ছোটোবেলায় আমার দু-বোনকে দেখেছি তারাব্রত করতে। তাদের মতো তাদের সমবয়সি মেয়েরাও করত এ ব্রত পালন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে। কত আকাঙ্ক্ষা কত আকুতিই না প্রকাশ পেত ব্রতচারিণীদের উচ্চারিত ছড়া-মন্ত্রের কলিতে কলিতে। পৌষ সংক্রান্তি থেকে মাঘ মাসের সংক্রান্তির দিন পর্যন্তও চলত এই ব্রতচার। পরিষ্কার উঠোনে আঁকা হত কত সুন্দর আলপনা। সে অলপনার ঘরে দাঁড়িয়ে তারা-বন্দনার গান গাইত আমার দু-বোন ছড়া কেটে কেটে। কী মিষ্টিই না লাগত তা শুনতে আর কী অপূর্ব পরিবেশই না সৃষ্টি হত শীতের সন্ধ্যায়! আজও মনে পড়ে গভীর মনোযোগ দিয়েই আমি শুনতাম তারাব্রতের মাহাত্ম-কথা আমার বোনেদের মুখে। তারা সুর করে বলত,
তারা পূজলে কী বর পায়?
ভীম অর্জুন ভাই পায়,
শিবের মতো স্বামী পায়,
কার্তিক গণেশ পুত্র পায়,
লক্ষ্মী সরস্বতী কন্যা পায়,
নন্দী ভৃঙ্গী নফর পায়,
জয়া বিজয়া দাসী পায়।
তারা পূজি সাঁজ রাতে,
সোনার শাঁখা পরি হাতে।
হায়, এত বর লাভের প্রত্যাশা সত্ত্বেও আমার পুববাংলার মা বোনেদের আজ কী হাল? তাদের ব্রত, তাদের সমস্ত শুভকামনা কবে সার্থক হবে? কবে আমরা আবার সগৌরবে গিয়ে ঘর বাঁধব আমাদের পুববাংলায়?
.
রামভদ্রপুর
যে দেশের জন্যে আমি হা-হুঁতাশ করছি সে দেশ আজ আর আমার নয়! স্বভূমি, স্বদেশ আজ আমার পরভূমি হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে দেশে জন্মেছি, যে দেশের ধূলিকণা আমার শরীর গড়েছে, যে দেশের নদীর জল, গাছের ফল আমাকে এত বড়োটি করেছে সে দেশের ওপর আমার আজ কোনো দাবিই নেই ভেবে মনটা হু হু করে উঠছে। ফুল না ফুটতেই ফুল ঝরাবার খ্যাপামি এল কী করে বুঝতে পারি না হাজার চেষ্টা করেও। হয়তো এই অবস্থাটিকেই রূপ দেওয়ার জন্যেই কবিগুরু লিখেছেন,
‘কোন সে ঝড়ের ভুল,
ঝরিয়ে দিল ফুল
প্রথম যেদিন তরুণ মাধুরী মেলেছিল এ মুকুল।। হায় রে!
নবপ্রভাতের তারাসন্ধ্যাবেলা হয়েছে পথহারা।…
…হায় গো দরদি কেহ থাক যদি শিরে দাও পরশন।
এ কি স্রোতে যাবে ভেসে দূর দয়াহীন দেশে
কোনখানে পাবে কূল। হায় রে!’
সত্যি, প্রথম যেদিন এই মকুলমাধুরী মেলেছিল সেইদিনই উঠল জীবনসমুদ্রে ঝড়! সারাবেলা বীণার সুর বাঁধতে গিয়ে কঠিন টানে কেঁদে উঠে ছিন্ন তার যেন রাগিনী দিল থামিয়ে। জীবনের ছন্দে প্রস্তুত হতে গিয়ে ভাগ্যে ঘটল নির্বাসন। আজ মাঝে মাঝে মনে হয়, আমাদের এই নির্বাসন দন্ড হল কোন দোষে? নবপ্রভাতের তারা সন্ধেবেলায় পথহারা হল কেন? বিধাতার নিষ্ঠুর বিদ্রুপে আজ আমরা সর্বহারা’ নামে পরিচতি। সর্বত্র নাসিকাকুঞ্চন ছাড়া অন্য পুরস্কার তো কপালে জুটল না! অবাঞ্ছিত হয়ে আর কতকাল আত্মার অবমাননা করব? স্রোতে কি বৃথাই যাব ভেসে, কূলে তরি কি কোনোদিনই লাগবে না? এই পথের ধার থেকে তুলে কোন দরদি মানুষ গৃহে দেবে স্থান তা জানি না!
নিজের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল আমার গ্রাম রামভদ্রপুরের কথা। মরুভূমির মাঝখানে নামটি যেন মরুদ্যানের শান্তির প্রলেপ এনে দেয় মনে। মাদারিপুর মহকুমার অধীনে, মেঘনার এক অখ্যাত শাখানদীর পশ্চিমে নতমুখে সহস্র লাঞ্ছনা মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছে আমার জন্মভূমি রামভদ্রপুর। আজ মাঝে মাঝে স্বপ্নের মধ্যে আমার গ্রামের ডাক শুনি; আমাদের ফিরে যাওয়ার জন্যে যেন আকুল মিনতি করছে সে। শুনেছি ভোরের স্বপ্ন মিথ্যে হয় না, আমার দেশজননী আমাদের কোলে টেনে নেবেন ভেবে মন নেচে উঠছে পেখম তুলে। যাব, নিশ্চয়ই যাব আমরা ফিরে মায়ের কোলে। আমরাও তত দিন গুনছি আশাপথ চেয়ে। আবার আমরা ভাইয়ে ভাইয়ে গলা জড়িয়ে সুখ-দুঃখের গল্প করব আগের দিনের মতো।
মনে পড়ছে আমাদের গ্রামের বাজারের কথা। নদীর ধারে বসত বাজার। এই বাজারে হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে কেনাকাটা করত জিনিসপত্র। দোকানপাটগুলো ছিল মানুষের যেন মিলনতীর্থ, সবাইকে বেঁধে রেখেছিল বন্ধুত্বের সুতোয় একত্রে। কেরামতের মশলার দোকানের খরিদ্দার ছিলাম আমরা, আবার বিখ্যাত হরলালবাবুর দোকানে রিয়াজদ্দি, দিনালি, মোবারক মুনশি আড্ডা দিত দিনরাত। সম্প্রদায় হিসেবে দোকান নির্বাচনের জঘন্য মনোভাব কোনোকালেই আমাদের ছিল না। মনে পড়ছে মাছ কেনার সময় ঠোঙার প্রয়োজন হলে অকুতোভয়ে চলে যেতাম কেরামতের দোকানে। একদিনের জন্যেও তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে দেখিনি। আবার অন্য দিকে, রিয়াজদ্দির কোনোদিন তরকারি বিক্রি না হলে সোজা সে নিতাই কুড়ির দোকানে বা হরলালবাবুর মুদিখানায় গিয়ে ডালাভরতি তরকারি রেখে দিত পরের দিন বিক্রি করার আশায়। বেতের ডালাখানি চৌকির নীচে রাখবার সময় সে হয়তো মুচকি হেসে কোনো কোনো দিন বলত—’কর্তা, থুয়ে গেলাম ডালাটা। আপনার তরকারির দরকার নাই? লাগে তো কন থুইয়ে আসি বাড়িতে। পয়সা হেইটা কাইল দিবেন কর্তা।’ গ্রামবাসীর ওপর গ্রামবাসীর এই যে সহজ বিশ্বাস, সে বিশ্বাসের গলা টিপল কে?
বর্ষাকালে বাজারে যাওয়ার পথে জল উঠত জমে। গ্রামের লোকজন তখন ভাসিয়ে দিত নৌকার শোভাযাত্রা। যারা কষ্ট করে হেঁটে যাওয়ার দুঃসাধ্য চেষ্টা করত তাদের ডেকে মুসলমান ভাইরাই আত্মীয়তার সুরে বলত,–‘কর্তা গো যাইতে কষ্ট হইব–নৌকা যোওন লাগে।’ মনে পড়ে ছোটোবেলায় দুষ্টুমি করে দলবেঁধে তাদের নৌকো চেপে পাড়ি দিতাম অন্য গ্রামের দিকে সকলের অজ্ঞাতে। কখনো বা নৌকো দিতাম ভাসিয়ে স্রোতের মুখে। নৌকার মালিক ঘাটে নৌকা না দেখে আঁতিপাঁতি করে খুঁজে বেড়াত এদিক-ওদিকে। কিন্তু এজন্যে তাদের মুখ মলিন হতে কোনোদিন দেখিনি, নৌকো খোঁজার পরিশ্রম কোনোদিন তাদের অসহিষ্ণু করে তোলেনি।
পিচ্ছিল কর্দমাক্ত পথে মুসলমানেরা যখন মাথায় তরকারির বোঝা আর হাতে দুধের হাঁড়ি নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠত তখন আমি, কুমুদ, মাখন, সতীশ প্রভৃতি ছেলেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তাদের মোট নিজেদের মাথায় তুলে নিয়ে সাহায্য করেছি। বাবুদের সাহায্য করতে দেখে তারা সভয়ে কত সময় দ্বিধাজড়িত গলায় বলেছে—‘এটা করেন কী কর্তা, আমিই নিতে পারুম’ এইভাবেই চলে এসেছে আমার গ্রামের দৈনন্দিন জীবন। সেদিনের সরল সহজ জীবন কি আমরা চেষ্টা করলে আবার ফিরে পেতে পারি না?
বাজারের পাশেই ছিল মধ্য ইংরেজি স্কুল। সামনে ছোটো মাঠ, তার পরেই মেঘনা নদীর শাখার উত্তালতরঙ্গমালা যেন সমস্ত বাধাবিপত্তিকে চূর্ণ করে কূলে এসে আছড়ে পড়ার সাধনায় ব্যস্ত। লাল-নীল-বাদামি-হলুদ পাল তুলে চলে নৌকার ঝাঁক,–দূর থেকে ময়ূরপঙ্খি বলে ভুল হয়। হয়তো এপার দিয়ে পাট বোঝাই নৌকা তিন হাজার মন মাল নিয়ে চলেছে। গুণ টেনে। মাঝিদের পেশিবহুল কালো কালো শরীর বেয়ে ঝরছে স্বেদধারা। গুণ টানার পরিশ্রমে পিঠের শিরগুলো উঠছে ফুলে। পরিশ্রমও যে মানুষকে সময় সময় কত মনোরম করে তোলে তার পরিচয় আমরা সেদিন পেয়েছি। মাঝিদের লোভনীয় স্বাস্থ্যের সঙ্গে নিজেদের ক্ষীণ শরীর মিলিয়ে কত সময় লজ্জিত হয়েছি মনে মনে।
গ্রামের ধনী ঈশানচন্দ্র দে মশায়ের ছেলে ললিতমোহন দের অর্থে তৈরি হয়েছিল আমাদের গ্রামের মধ্য ইংরেজি স্কুলটি। টিনের ছাউনি দেওয়া লম্বা বাড়ি, সমস্ত গ্রামের বিদ্যাবিতরণ কেন্দ্র। নীচের ক্লাসে আমার সঙ্গে পড়ত আকুবালী আর ফজলুল বলে দুজন সহপাঠী। তিনজনের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা থাকার দরুনই হয়তো আমরা তিনজনের বন্ধুত্বের ত্রিভুজ গড়ে ছিলাম সেদিন। ওদের ফুলকাটা সাদা টুপি, আর রঙিন ভেলভেটের ফেজ দেখে কত সময় মন খারাপ করে ঘরের এককোনায় বসে থেকেছি–আমাকে মনমরা হয়ে থাকতে দেখে ওরা কত সাধ্যসাধনা করেছে কারণ নির্ণয়ের জন্যে। পরে কারণ জানতে পেরে হেসে নিঃস্বার্থভাবে নিজেদের টুপি দিয়েছে আমার মাথায় চড়িয়ে। মুহূর্তে মনের মেঘ কেটে গিয়ে দেখা দিত হাসির সূর্ব। তাদের টুপি মাথায় দিয়ে তাদেরই সঙ্গে খেলা করেছি কতদিন। কিন্তু আজ? জাতিভেদের সংকীর্ণ গন্ডির মধ্যে আর পারবে কেউ এমনভাবে অন্যের মুখে হাসি ফোঁটাবার জন্যে নিঃস্বার্থ ত্যাগ করতে?
মনে পড়ে আকুবালী আমাদের বাড়ি এলে মা ওকে আম, কলা, দুধ দিতেন বাটি ভরে। আকুবালী আকণ্ঠ ভোজন করে স্বহস্তে বাটিটি ধুয়ে রাখত বারান্দায়। বারণ করলেও শুনত না। জানি না কোথা থেকে আকুবালী শিখেছিল এ ধরনের সামাজিক শৃঙ্খলা! আমাদের খাওয়ার সময়েই হয়তো কোনো কোনোদিন এসে পড়েছে করিমচাচা কিংবা জয়নাল। থপ করে চাটাইয়ের ওপর বসে পড়ে আকুবালীর দিকে রাগত দৃষ্টি হেনে বলেছে—’তুই তো খাইয়া লইলি পেটটা ভইরা, আমরা পেটটা ভরুম না? দেননা মাঠাইন দুইটা আম খাইয়া লই। কর্তাগো সিন্দুইরা গাছের আমগুলা বড়ো মিষ্টি!’ কত আনন্দ করেই না মা খাওয়াতেন তাদের। আজও হাসি পায় তাদের ভোজনপর্বের দৃশ্যটা মনে পড়লে। আগ্রহ ভরে চেটে চেটে আম খাওয়ার ঢং দেখলে মনে হত যেন বহুদিন থেকে ওরা উপবাসী! খাওয়ার পরেই কলকেতে ভরে নিত তামাক।
এই যে সামাজিক হৃদ্যতা সেদিন দেখেছি তার মৃত্যু হল কোন চক্রান্তকারী ডাইনির মন্ত্রে? মানুষ মানুষকে কেন আজ এড়িয়ে চলছে পশুর মতো? আমরা কি স্বার্থপরতা, নীচতা, শঠতা ভুলে গিয়ে আবার আত্মীয় হয়ে উঠতে পারি না? সাধারণ মানুষ কেন হিংস্র হবে, কেন মানবীয় গুণগুলোকে বিসর্জন দিয়ে পরের ক্রীড়নক হয়ে উঠবে? কাকে ছেড়ে কার চলে সংসারে? আবার কি আমরা মানুষ হতে পারব না, একত্রে মিলেমিশে থাকতে পারব না?
প্রতিবৎসর বাসন্তি পুজো হত আমাদের বাড়িতে। এ পুজো উপলক্ষ্যে গ্রামের ধনী-মানী জ্ঞানী-গুণীর নিমন্ত্রণ তো হতই, সেই সঙ্গে নিমন্ত্রণ হত সমস্ত গ্রামবাসীর। এ উৎসবে দেখেছি আমাদের চেয়ে বেশি উৎসাহী ছিল মুসলমান ভাইরা। এই দিনটির জন্যে তারা উদগ্রভাবে প্রতীক্ষা করে থাকত বছরের প্রথম দিন থেকে। তাদের আগ্রহে পুজো যেন আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। তারাই সংগ্রহ করে আনত বলির মোষ। নিয়ে আসত চাঁদপুর থেকে মালপত্র সুশৃঙ্খলভাবে। পুজোর ঢাকের আওয়াজে সমস্ত গ্রামখানি হয়ে উঠত জীবন্ত, বহুদূর থেকে ঢাকের শব্দ শুনে লোক আসত ছুটে। এ পুজোকে প্রত্যেকে নিজের বলে গ্রহণ করায় সেদিন কোনোরকম গোলযোগই দেখা দিত না গ্রামে। গ্রামবাসীদের মধ্যে আত্মীয়তাপূর্ণ ব্যবহারই সমস্ত জিনিসটিকে করে তুলত মধুময়।
আমাদের বাড়িতে থাকত জংগু ঢালি আর এলাহিবক্স। তারা বাগান তদারক করত, কাঠ চিরত, নৌকা বাইত-বলতে গেলে কঠোর পরিশ্রমের সব কাজগুলোই তারা সমাধা করত বিনা বাক্যব্যয়ে। সকালবেলা একগামলা পান্তাভাত খেয়ে লেগে যেত কাজে। ভাত খাওয়ার ব্যঞ্জনও ছিল তাদের কত অনাড়ম্বর–একটি পেঁয়াজ আর একগন্ডা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে এত নির্বিবাদে এত ভাত খাওয়া যেতে পারে তা এলাহিবক্সদের খাওয়া না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না! জীবনযাত্রা এত সরল ছিল বলেই তাদের পক্ষে সবই সেদিন ছিল সম্ভব, কিন্তু আজ আর সেদিন নেই। বিলাসের ফাঁসে পড়ে সকলেই হয়ে উঠেছে বিলাসী, এখন সারল্য তাই হয়েছে বিতাড়িত। আগে যারা কর্তাবাড়ির প্রসাদ পেয়েই নিজেদের মনে করেছে ধন্য, আজ তাদের মনোভাব অন্য ধরনের। এই প্রসঙ্গেই মনে পড়ছে আম কুড়োনোর ছবি। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে বাগানে আম কুড়োতে গেলে জংগু আর এলাহিবক্স কত সমাদর করে আমাদের হাতে আম দিত তুলে। বাগান জমা দেওয়া সত্ত্বেও তারা আপনা থেকে কোনোদিনও একটি আম নেয়নি, সমস্ত আম পৌঁছে দিয়েছে আমাদের বাড়িতে। কর্তামা বা বাড়ির অন্য কেউ ডালায় ভরে যে কটা আম তাদের দিতেন তাই বাড়ি নিয়ে যেত তারা হাসিমুখে পরমপরিতৃপ্তির সঙ্গে। ডালা কাঁধে তুলতে তুলতে বরঞ্চ কৃতার্থ হয়ে বলত, ‘পোলাপানেরে থুইয়া আমি একলা খামু কেমন কইরা, আপনাগো দয়াইত তবু পোলাপানরা আম জাম খাইতে পায়।’ একথা কি বঞ্চিতের কথা? আজ ভারাক্রান্ত মনে ভাবি সময় সময় মানুষের সৌহার্দ্যবোধ কেন নষ্ট হল? আমাদের আত্মীয়তাবোধ কি তাহলে চোরাবালির ওপর ছিল প্রতিষ্ঠিত, না হলে, তা এমন অতলতলে তলিয়ে গেল কী করে হঠাৎ?
মনে পড়ে আমাদের বাড়ির সর্বজনীন তামাক খাওয়ার দৃশ্যের কথা। ঘরের বারান্দায় থাকত তামাকের সাজসরঞ্জাম। বাজারের পথে বাড়ি হওয়ায় চব্বিশ ঘণ্টা ভিড় থাকত লেগে। যে কেউ তামাক খেত, তার শাকরেদ হত জংগু আর এলাহি। বিনামূল্যে এই সামান্য তামাকের আকর্ষণ ছিল অদ্ভুত, যতক্ষণ ধোঁয়া না পেটে পড়ত ততক্ষণ সবাই যেন স্থবির হয়ে বসে থাকত গোলাকার হয়ে! বিদেশি পথিকরাও শ্রমলাঘবের জন্যে এখানে ক্ষণিকের জন্যে না বসে যেতে পারত না। আশ্চর্য হয়ে লক্ষ করেছি সেদিন নেশার কাছে সমস্ত জাতিভেদ হয়েছিল পরাজিত। সেটা ছিল মানুষের বিশ্রামাগার, ঘর্মক্লেদাক্ত দেহে রৌদ্রের খর তাপ থেকে বিশ্রাম নেওয়ার জন্যেই আত্মীয়তার সুর উঠত নিবিড় হয়ে বেজে। ধোঁয়ার অক্ষরে অক্ষরে সেদিন লেখা হত–’সবার উপর মানুষ সত্য, তাহার উপর নাই!
শৈশবের কোমল মনে যে ছাপ একবার পড়ে তা হয়ে থাকে অক্ষয়। এখন হুবহু মনের মানচিত্রে সমগ্র গ্রামখানি জ্বলজ্বল করছে। মনে পড়ে বাজার থেকে পশ্চিম দিকে চলে গেছে প্রশস্ত রাস্তাটি–তার দু-পাশে কুমোর, নাপিত, কামার ইত্যাদি নানা শ্রেণির বাস। আধ মাইল যাওয়ার পর ডাইনে বাঁয়ে বেঁকে গিয়ে গাঁয়ের দু-পাড়া এসে মিশেছে চৌমাথায়। এই মোড়টিই গ্রামের কেন্দ্রস্থল। ডাইনের রাস্তাটি মুসলমান পাড়ার বুক চিরে চলে গেছে কার্তিকপুর পর্যন্ত, বাঁয়ের রাস্তা গেছে গ্রামের উচ্চশ্রেণির বাবুমশায়দের পাড়া ছুঁয়ে। এই রাস্তার ওপরেই পড়ে মুন্সেফ সাহেবের বাড়ি, নাম ‘বাবুবাড়ি’। ঝাউগাছ সমন্বিত প্রশস্ত খোয়া বাঁধানো চওড়া রাস্তাটি বাবুবাড়ির আভিজাত্যের পরিচায়ক। সেদিন ঝাউগাছের বুক থেকে সোঁ সোঁ শব্দ করে যে হাওয়া যেত ছুটে আজ সে শব্দ শুনলে মানুষের আর্তনাদ বলেই ভুল হবে! মনে হবে সহস্র দুঃখ-দুর্দশায় বুক ফাটানো আর্তনাদ ফেটে পড়ছে ঝাউগাছের ফাঁকে ফাঁকে। জানি না মুন্সেফ সাহেব সে দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেয়েছেন কি না! রাবণের চিতাগ্নির মতো এই যে মনের আগুনের আর্তস্বর অহর্নিশি শব্দায়িত হচ্ছে এর শেষ কোথায়?
এখানেই পুজোর সময় হত থিয়েটার। থিয়েটারের জন্যে সমস্ত গ্রামবাসীরাই উদগ্রীব হয়ে দিন গুনত, চাঁদা তুলত, হাতে লিখে প্রোগ্রাম তৈরি করত। পুজোর ছ-মাস আগে থেকেই সিনগুলো নতুন হয়ে ঝলমলিয়ে উঠত। গ্রামের চিত্রকর মল্লিকমশায় ছিলেন এই দৃশ্যপট সজ্জার পান্ডা। তিনি দৃশ্যপটে আঁকতেন। রামভদ্রপুরেরই গ্রাম্য ছবি। আমার গ্রামের ছবি ড্রপসিনের গায়ে কী চমৎকার লাগত তা আজ ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না।
পুজোর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে মহীসারের বৈশাখী মেলার কথা। বৈশাখের প্রথম দিন থেকে সাত দিন সে মেলা হত স্থায়ী। আমরা গুরুজনদের কাছ থেকে পৃথক পৃথক ভাবে পয়সা জমিয়ে মেলা দেখতে যেতাম হইহুল্লোড় করে। চৈত্র সংক্রান্তিতে সুদূর হাটখোলার একমাইল উত্তরে সারাদিন মেলায় কাটিয়ে বাড়ি ফিরতাম ক্লান্ত চরণে। হাতের পুঁটলিতে বাঁধা থাকত পুতুল, বাতাসা, কদমা, জিলিপি, বাদামভাজা ইত্যাদি লোভনীয় বস্তুসম্ভার। মহীসারের মেলাতে রবারের বল, মাটির গণেশ আনতেই হবে এই ছিল আমাদের নিয়ম। সেসব দিন কি আমাদের জীবনে আর ফিরে আসবে না? এই মেলা উপলক্ষ্যে আমাদের গ্রামে বাইচ খেলা ছিল প্রধান আকর্ষণ। শান্ত মেঘনার শাখানদীতে বাইচ খেলা সেদিন সমস্ত গ্রামবাসীকে উদ্দীপনা দিয়েছে তার তুলনা পাওয়া ভার। নদীর তীরে একটা দীর্ঘ বাঁশে পেতলের একটি কলসি থাকত ঝুলানো। বাইচ আরম্ভ হলে দ্রুত নৌকো চালিয়ে যে প্রতিযোগিতায় জিতে ওই কলসি নিতে পারবে তারই শ্রেষ্ঠত্ব সকলে নিত স্বীকার করে। চক্ষের পলকে তীব্র গতিতে নৌকোগুলো সব হয়ে যেত অদৃশ্য। নদীর বুকে কালো কালো বিন্দু যেন ছুটে চলেছে, সহস্র চোখে তারই দিকে তাকিয়ে থাকত অজস্র মানুষ। উৎসাহের বাষ্পে ফেটে পড়া সে মানুষের আজ এ কী অবস্থা! যারা একদিন আনন্দকেই জেনেছিল জীবন বলে, আজ তারা উলটো পথের পথিক হল কেন? উপনিষদ বলছে যে আনন্দ থেকেই মানুষের জন্ম, আনন্দের মধ্যেই তার লয়। কিন্তু আমরা তো তার প্রমাণ পেলাম না! আনন্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করলেও আনন্দের মধ্যে তো বিদায় নিতে পারলাম না। তবে কি স্বর্গ থেকে এ বিদায় ক্ষণস্থায়ী? আবার আমরা আনন্দের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হব? মহাজন বাক্য তো নিষ্ফল হয় না, অবিশ্বাসী আমরা সব সময় স্থির মস্তিষ্কে চিন্তা করতে পারি না বলেই অযথা দুঃখ পাই। উপনিষদ সত্য, উপনিষদ অভ্রান্ত, উপনিষদের কথা নিষ্ফল হতে পারে না। আবার আমরা মানুষ হব, আবার আমরা সুখী-স্বচ্ছল হব। একাগ্রমনে কান পেতে শুনুন, আকাশে বাতাসে উঠছে আনন্দের সুর। আনন্দের মধ্য দিয়ে আনন্দকে চিনে নেওয়াই কর্তব্য আমাদের।
.
কাইচাল
পুজোর ছুটি। ‘ঢাকা মেল’ ধরবার জন্যে ছুটে চলেছি। স্টেশন একেবারে জনারণ্য। তবু এ ভিড় অগ্রাহ্য করেই প্রতিবার বাড়ি যাওয়ার জন্যে উন্মুখ হয়ে রওনা হয়েছি। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে শেয়ালদা থেকে ট্রেন বেরিয়ে গেল। কলকাতার আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে চলেছি। চেনা চেনা গ্রাম ও শহরের পাশ দিয়ে হু হু করে এগিয়ে চলেছে ট্রেন। গ্রামের কাছাকাছি এসে পড়েছি। আমার গ্রাম আমাকে ডাকছে ফরিদপুর জেলায় কাইচাল আমার গ্রাম।
ট্রেন থেকে নেমে নৌকোঘাটায় গিয়েছি, অমনি শত কণ্ঠে চিৎকার হয়েছে—’কোহানে যাবেন কত্তা, এদিকে আসেন।’ যে নৌকোখানি দেখতে একটু ভালো, গেলাম তার নিকট। মাঝির নাম মৈনুদ্দিন, এই তার আসল পেশা আর এমন বিশ্বাসী সে যে, নৌকোয় কিছু ফেলে গেলেও ফিরিয়ে দিয়ে যায়, সুতরাং ভাড়ার প্রশ্নই উঠল না।
নৌকো চলেছে। নৌকোর বাইরে বসে আছি, সব দেখছি। মাঝি বললে,–‘কর্তা, ছইর মধ্যে যান রইদ লাগবে।’ অবসন্ন দেহ, তবু ঝিম ধরে বসে আছি, কী যে এক অনাবিল আনন্দ অনুভব করছি। ফরিদপুরে ‘মাইজা মিয়ার খাল’ বিখ্যাত, তার মধ্যে নৌকো পড়েছে। মৈনুদ্দিন মাথাল নামিয়ে রেখে মাজার গামছা কষে নিল। চইরটাকে একটানে বের করে নিয়ে এক চিৎকার দিয়ে বলল, ‘যার যার হাতের বায়ে।’ তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলাম, দেখি কিছু সাহায্য করতে পারি কি না। মৈনুদ্দিন দিল না, বলল—’আপনার নাগবে না, আপনি বসেন।’
নৌকো ছেড়ে দিলে, জিজ্ঞাসা করি কখন পৌঁছোতে পারব। সে বললে, সন্ধ্যাসন্ধি। পাট ভরতি, মুসুর ভরতি, আরও কতরকম পসরা ভরতি কত নৌকো ঝুপঝাঁপ শব্দে চলেছে নিকটবর্তী কোনো এক বন্দরের হাটে।
ঢাকের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বুঝলাম এসে পড়েছি, তবে আশপাশে ছোটো ছোটো আরও গ্রাম রয়েছে, তাই আমার গ্রাম কতদূর তা বুঝতে পারছি না! মৈনুদ্দিন বলল,–‘এই তো কাইচালের বিল, এটা পার হলেই আপনাগো গ্রাম দেহা যাবেনে।’
কাইচাল গ্রামের বাবুদের বিল। এর অনেক ইতিহাস আছে। আশপাশে ভূত-পেতনি ঘোরে আর বিলের মধ্যে সিন্দুকের ঘড় ঘড় শব্দও নাকি অনেকে শুনেছে। ফইটকার খালের মুখে একটা ভ্যাসালের কাছে গেলাম। সনাতন মাঝির ভ্যাসাল, ওপরে সে আছে, একটা ছোটো হ্যারিকেন লণ্ঠন বাঁধা। মাছটাছ আছে নাকি সনাতন?’ বলতেই একখান চার-পাঁচ সের ওজনের নলা এবং সের আড়াই পরিমাণ টাটকানি দিল সে। বলল, ‘লইয়া যান, দাম এখন দেওয়া নাগবে না। খালের ভেতর দিয়ে একখানা মুসলমান গ্রাম পার হতেই কানে ভেসে এল দোতারার ক্ষীণ শব্দ, বুঝলাম আমাদের গ্রামের নাপিতপাড়ার প্রসন্ন শীল। এ তল্লাটে ও ছাড়া আর কেউ এ যন্ত্র বাজায় না। আর জানতাম কর্মক্লান্ত দিনের শেষে রোজই ও দোতারা বাজায়। হঠাৎ ‘কাহার’ বাড়ির আলো দেখলাম, প্রশ্ন এল, ‘যায় কেডা?’ নৌকো গিয়ে ঘাটে লাগল।
গল্প শুনেছি যাতে বাইরের কোনো শত্রু কোনো হিন্দুর গ্রাম আক্রমণ করতে না পারে এইজন্যে এ তল্লাটের প্রায় প্রত্যেকখানি গ্রামই চতুর্দিকে মুসলমানদের দিয়ে ঘেরা। আমাদের গ্রামখানিও তেমনি। বহুপুরাতন গ্রাম, জমিদার প্রধান স্থান। কালীমন্দির শিবমন্দির, পুরোনো দিঘি, রামসাগর, শানবাঁধানো ঘাট ইত্যাদিতে তার সাক্ষ্য দেয়। বসু মজুমদারেরা পুরাতন বাসিন্দা। ছেলেগুলো উচ্চশিক্ষা পাওয়ায় সবাই প্রবাসী। তাই নাটমন্দিরের ওপরে উঠেছে বট পাকুড় গাছ, ভেতরে বাস করেছে কবুতর আর পেঁচা, তবু কিন্তু কোনো পুজো-অর্চনা বাদ যায় না।
প্রায় সমস্তরকমের জাতের বাস আছে এ গ্রামে। ভদ্র এবং শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশি থাকায় আশপাশের সমস্ত লোকের আচার-ব্যবহার ভদ্র। উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত গৃহস্থের প্রায় সকলেরই ধানের গোলা, গাইগোরু এবং পুকুর আছে। তারপর প্রত্যেকখানি বাড়িই আম, নারিকেল, কলা, কাঁঠাল ইত্যাদি গাছে ঘেরা; প্রত্যেকের সঙ্গেই যেন নিবিড় আত্মীয়তার বন্ধন। প্রত্যেকটি ঋতু উপভোগ করেছি পরিপূর্ণভাবে, কোকিলের কুহু কুহু রব, দোয়েলের শিস, পাপিয়ার তান। প্রকৃতিদেবী যেন আপন হাতেই সাজিয়েছেন গ্রামকে। উত্তর এবং দক্ষিণে প্রশস্ত মাঠ। শীতের দিনে দেখেছি পরিপূর্ণ যুবতীর ন্যায় মাঠখানি নানারকম রবিশস্যে ভরা–আবার বর্ষাকালে দ্বীপের ন্যায় মনে হয়েছে গ্রামটিকে। শীতের দিনে কাদের গাছি এসেছে খেজুর গাছে হাঁড়ি পাততে। ছেলেদের দল ছুটেছে তার পেছনে পেছনে,–‘ও গাছি একটা চুমড়ি দেবে?’ গাছি বলেছে, ‘পান নইয়া আইস।’ তার সাজ দেখলে মনে হত যেন সে কোনো যুদ্ধে যাচ্ছে।
নির্মল ঘোষ, বিমল ঘোষমহাশয়রা বাড়ি আসছেন শুনলে সারাতল্লাটে সাড়া পড়ে যেত। আশপাশের গ্রামের লোকজন উদগ্রীব হয়ে উঠত দেখা করবার জন্যে। গ্রামের ছেলে-মেয়েরা হয়ে উঠত চঞ্চল। খেলাধুলোর বন্দোবস্ত হত সকালে, দুপুরে, বিকালে–যাতে কেউ বাদ না যায়। সে কী আনন্দ! প্রত্যেকেই কিছু না কিছু পুরস্কার পেত। গ্রামের পূর্বদিকে সাত-আট মাইল দূর থেকে নির্মলবাবুর প্রতিষ্ঠিত স্কুল ঘর দেখে লোকে ‘ওই কাইচাল’ বলে এ গ্রাম ঠিক করে। কয়েক বৎসর হল একটি দাঁতব্য চিকিৎসালয়ও তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ ছাড়া দেশের ও দশের অনেক উপকার এবং কাজ এঁরা করেছেন। এঁদের কাজকর্ম দেখে সকলেই বলাবলি করত, লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধারের জন্যে এঁরা দু-ভাই দৃঢ়সংকল্প।
এঁরা যখন চলে এসেছেন তখনও নির্জীব হয়নি গ্রাম। ছোটো হিস্যার খোকাদার কাছারিঘরের দোতলায় প্রায় সব সময় চলেছে নাচের মহড়া–এক, দুই, তিন। বড়ো হিস্যার কাছারিতে চলেছে নামকরা অভিনেতাদের পার্ট, কত অঙ্গভঙ্গি সহকারে মাস্টার তাদের শেখাচ্ছেন। তারপর মণীন্দ্রমোহন বসু মজুমদারের কাছারিতে চলেছে গান-বাজনার তোড়জোড়।
গ্রামে ছিল পোস্ট-অফিস। দূর গ্রাম থেকে কোনো লোক এসেছে দরকারে, যত শীঘ্র সম্ভব ফিরে যাবে; কিন্তু ভুলে গেছে সে তার জরুরি কাজ। একাছারি ওকাছারি ঘুরে দেখেশুনে ডাকঘরে যেতে যেতে ডাকঘর হয়ে গেছে বন্ধ!
গ্রামের মোহন শীল বিকট কালো পোশাক পরে কপালে বড়ো একটা সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে খাড়াহাতে জল্লাদের ভূমিকায় যখন থিয়েটারের আসরে অবতীর্ণ হয়েছে তখন অনেক ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়ে ভয়ে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে। খোকাদার প্রকান্ড আটচালা ঘরে হচ্ছে যাত্রাগান–গ্রামের রাশভারী প্রকৃতির লোক সুরেশচন্দ্র ঘোষমহাশয় দলের সেক্রেটারি, দক্ষিণারঞ্জন বসুমহাশয় ম্যানেজার, শ্রোতার সংখ্যা অধিকাংশই মুসলমান, কিন্তু ‘টু’ শব্দটি নেই। কারণ জমিদার বাড়িতে গান, তারপর স্বয়ং জমিদাররা উপস্থিত। জায়গায় জায়গায় পেয়াদা এবং বরকন্দাজরা বাঁশের এবং বেতের লাঠি হাতে দন্ডায়মান হয়ে খবরদারি করছে।
যখন চড়ক পুজো এসেছে, তখন কী মাতামাতিই না শুরু হয়েছে। বালা সন্ন্যসীরা নানারূপ কৃচ্ছসাধন করে এই জাগ্রত এবং ক্রুদ্ধ দেবতার পুজোর জন্যে তৈরি হয়েছে। খোকাদার বেলতলা পুকুরের মধ্যে প্রকান্ড একটি আস্ত গাছ ডুবে আছে–যে সে গাছ নয়, ওর ভেতর রয়েছে দেবতা! প্রবাদ আছে চড়ক পুজোর ঢাকের বাজনা শুনলে ওই গাছ ভেসে ওঠে। এই পুজোর দিন যত সব ভূত, পেতনি, দানব, দত্যি নেমে আসে এবং অবাধে যাতায়াত করে; তাই ওইদিন আগে থেকেই সাবধান হয় ছেলে-মেয়েরা।
গাজন গান হবে। গ্রামের অক্ষয় পাল এবং নগরবাসী মন্ডল পুরাণ আলোচনার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছে, কতলোক জমেছে। জ্ঞানীজন সব বসেছে সম্মুখে, পাশে দুটো ঢাক তৈরি হয়ে রয়েছে। হচ্ছে গাজন গান, কী সে আনন্দ! একবার শ্যাওড়া গাছের ডাল কাটায় গ্রামের একটা ছেলে ভীষণ অসুখে আক্রান্ত হয়। বাঁচবার আশা তার মোটেই ছিল না। পরে প্রকৃত ঘটনা জেনে মানত করে পুজো দেওয়া হয় গাছের গোড়ায়। তারপর সে রোগমুক্ত হয়। আমি নিজে দেখেছি। কাজেই অবিশ্বাস করতে পারি না। তবে হতে পারে কাকতালীয়।
বীজ বপনের সময় বৃষ্টির পাত্তা নেই। সারামাঠ প্রখর রৌদ্রতাপে ফেটে খাঁ খাঁ করছে। কৃষককুল হায় হায় করছে। অহোরাত্র কীর্তন হচ্ছে। হঠাৎ কেউ বলল গ্রামের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত নিশাতলা–ওখানকার দেবতা স্বপ্নে বলেছে পুজো দিতে! অমনি সবাই মিলে সেখানে গিয়ে দেবতার পুজো দেয়, তিন-চার মন দুধ দিয়ে যে যে গাছে দেবতা আছে তাদের স্নান করায়। আমরা দেখেছি সেই দিনই কি পরের দিন ভীষণ বৃষ্টি হয়ে মাঠ ভাসিয়ে দিয়েছে! বুদ্ধিতে এসবের ব্যাখ্যা চলে না। কী হিন্দু কী মুসলমান সবাই ওই জায়গাটিকে ভয় করে এবং ভক্তিও করে। হায়, আর কি কোনোদিন ফিরে যাব না সে দেশে, আমার সোনার গাঁয়ে!
কালীবাড়িতে আছেন জাগ্রত কালী, পাশে সাতটি শিব। প্রত্যহই পুজো হয়। আমরা শুনেছি আমাদের কালীবাড়িতে নরবলি পর্যন্ত হয়েছে!
ফাগুন মাস। কলকাতা থেকে সুধাংশুবাবু এসেছেন। অনেক গুলি এনেছেন। বাড়িতে তাঁদের বন্দুক আছে। ছেলের দল সব তৈরি হয়েছে ঘোড়ামারার বিলে পাখি শিকারে যাবে। কত আনন্দ এতে পেয়েছে গ্রামের ছেলেরা। তিন-চারটে বাতাবি লেবুর গাছ ছিল, কেউ কোনোদিন পাকা লেবু দেখেনি–কারণ ওসব দিয়ে ফুটবলের কাজ চালাতে হয়েছে।
পশ্চিমপাড়ার ঠিক কোনায় ছিল নগেন-ক্ষিতীশদের বাড়ি। তাদের মার সঙ্গে আমার মায়ের ছিল খুব ভাব। দুজনেই বিধবা। নিজের তিনটি ছেলে থাকা সত্ত্বেও কী ভালোই না বাসতেন তিনি আমাকে। প্রত্যেকদিনই গিয়েছি তাঁদের বাড়িতে আর কিছু মুখে না দিয়ে কোনোদিনই ফিরতে পারিনি। অনেকে মনে করিয়ে দিত, আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, কিন্তু মাসিমার অপত্য স্নেহের কাছে কোনো কথাই টিকত না। মনেপ্রাণে মাসির মুখে হাসি দেখতে চেয়েছি। নগেন ক্ষিতীশ থাকত বিদেশে। মাসির দুঃখ, তারা ঠিকমতো চিঠি দেয় না। নগেন বড়োভাই হয়েও ক্ষিতীশের বিয়ের জন্যে চেষ্টা করছে না, আরও কত কী মাসি নালিশ জানাত আমার কাছে। আজ নগেন, ক্ষিতীশ, মাখন তিনজনেই সংসারী হয়েছে, বেশ সুখে-শান্তিতেই আছে। কিন্তু মাসি তাঁর বউ আর নাতি-নাতনিদের নিয়ে দেশে থাকতে পারলে তাঁর কত বেশি আনন্দ হত!
তারপর বিশ্বকর্মা পুজোয় ভাঙার গাঙে নৌকাবাইচ। রতন সর্দার সকালেই তার বাবরি চুলে সাবান দিয়ে ফুলিয়েছে, কপালে বড়ো সিঁদুরের ফোঁটা দিয়েছে, লাল গামছা একখানা পরেছে, আর একখানা মাজায় বেঁধে এক হাতে ঢাল এবং অপর হাতে লকলকে ধারালো খঙ্গ নিয়ে নৌকোর ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে। আশিহাত লম্বা নৌকো, দশ-বারো হাত হবে তার গলুই। দু-পাশে পেতলের চক্ষু, আরও কত কী দিয়ে সাজানো। গলুই-এর ওপরে পেতলের দুটি সাপ ফণা তুলে রয়েছে এবং নৌকোর দোলায় দোলায় উভয়ে উভয়কে আঘাত করছে। রতন সর্দার বোল বলছে,
আমার নায়ে হোলক গাবি কে, আরে হোলাবিলাই শাদি করবে কাহই আইনা দে।
গ্রামের প্রত্যেক বাড়ির প্রত্যেকটি আমগাছের কোনো-না-কোনো নাম রয়েছে। আমাদের পুকুরপাড়ে উত্তর-পূর্ব কোণে ছিল একটা খুব উঁচু আম গাছ–নাম তার থোপঝুড়ি। ওই গাছের মাথায় ছিল বড়জিয়াল পাখির বাসা। তারা ওই স্বামী-স্ত্রীতে প্রহরে প্রহরে ডাকত। পুকুরপাড়ের গাছে ছিল মাছরাঙার গর্ত। মাছরাঙা পুকুর থেকে মাছ ধরে পেয়ারা গাছের ডালে বসে খেত। আমি বাঁশ-গুলি দিয়ে অন্য অনেক পাখি মেরেছি, কিন্তু এদের কোনোদিন মারিনিঃ |||||||||| পূর্বপাড়ায় ত্রিনাথের মেলা। কে যেন গান ধরেছে,-”আমার ঠাকুর তেন্নাথের যে করিবে হেলা…’, তারপর যেন কী ভুলে গেছি। গণশা গিয়েছে সেখানে, তাই কামিনীদি ডাকছে, ও গণশা, গরে সোমত্ত বউ, আর তুই গান শুনছিস?’ কামিনীদি শুতে যেতে পারছেন না। আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাঁর সেসব বিলাপ শুনতাম।
এখানে আমার ঘুম ভাঙানোর কেউ নেই, কিন্তু গ্রামের বাড়িতে আমার ঘরের কোণে বেতের ঝোপে ডাহুক ডাহুকি, আরও কতরকম পাখির ঐকতান ভোরে আমার ঘুম ভাঙাত। |||||||||| গ্রামের কথা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে বৃদ্ধ ঘোষালমশায়কে। তিনি যখন মাথায় কলসি নিয়ে অপরূপ ভঙ্গিতে নাচতেন, তখন গ্রামের কত লোক এসেছে তা দেখবার জন্যে। এখনও লোকমুখে সে নাচের খবর শুনতে পাওয়া যায়। |||||||||| অক্ষয় চক্রবর্তীমশাই চামর দুলিয়ে রামায়ণ গান করতেন। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সব
তন্ময় হয়ে বসে শুনত। রামের বীরত্বে কে না পুলকিত হয়েছে, লক্ষ্মণের কথায় কার না শরীরে রোমাঞ্চ দিয়েছে, সীতার দুঃখে কে না অভিভূত হয়েছে? কিন্তু আজ সেসব স্মৃতি!
আজকাল পঞ্চায়েত প্রথার কথা খুবই শুনছি। অথচ আমার গ্রামে এ সব সময়েই ছিল। আশপাশের কোনো গ্রামে বা কোনো লোকের সঙ্গে কারো ঝগড়া-বিবাদ হলে জমিদার বাড়ির পেয়াদা গিয়ে নিয়ে আসত তাদের খবর দিয়ে। গ্রামের প্রবীণ লোকদের ডাকা হত, জমিদার উপস্থিত থাকতেন, সূক্ষ্ম বিচার হত, উভয়েই খুশি মনে গল্প করতে করতে চলে যেত। এইভাবে কত লোক অযথা অর্থব্যয়ের হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলত। |||||||||| গ্রামের চতুষ্পর্শ্বে দু-তিন মাইলের মধ্যে ভাঙার হাট, পোড়াদিয়ার হাট, নরকান্দার হাট, ফলিখালির হাট আর আউরাকান্দির হাট-বর্ষাকালে দেখেছি কত লোক কত রকমের নৌকোয় করে ছুটেছে হাটের দিকে। আবার শুকনোকালে দেখেছি মাঠের ভেতর দিয়ে নানা রাস্তায় লোক ছুটেছে কাতারে কাতারে হাটের দিকে। কারও মাথায় ধামার ভেতর কয়েকটি লাউ কিংবা কিছু বেগুন, না হয়তো অন্য কোনো তরিতরকারি, কারও হাতে দুধের ভাঁড়। এরা সবাই আপন আপন খেত কিংবা বাড়ির জিনিস নিয়ে চলেছে হাটে। তারা ধানের দর, পাটের দর, ভাঙার হাটে কয়খানা ধানের নৌকো এসেছে ইত্যাদি বলাবলি করতে করতে চলেছে।
জমিদার বাড়িতে পুণ্যা হবে। কাছারিঘর সাজানো হয়েছে। ভোর হতেই প্রজারা সব আসছে দুধ মিষ্টি আর টাকা নিয়ে। এদিকে আটটায় সর্দারি খেলা হবে, নামকরা সব সর্দাররা এসেছে। কে কত ভালো খেলা জানে আজ তার প্রমাণ হবে স্বয়ং জমিদারের সামনে। আফা সর্দার কলসির ওপর থালা উপুড় করে বাজাতে আরম্ভ করেছে, আর আর সর্দাররা পা তুলে নেচে নেচে কতরকমের কায়দা দেখাচ্ছে। এসব দৃশ্য এখনও চোখে ভাসে।
.
খালিয়া
নদীর নাম কুমার, গাঁয়ের নাম খালিয়া। নামের মধ্যেই মূর্ত হয়ে রয়েছে নদীটির পরিচয়। কুমারের মতোই সংযত ও সাবলীল ছন্দে অবিরাম বয়ে চলেছে সে তার অনির্দেশ্য যাত্রায় মধুমতীর উদ্দেশে। তার যাত্রাপথের দু-ধারে রেখে যায় সে তার অকৃপণ দাক্ষিণ্যের পরিচয়। তার অফুরান প্রাণ-বন্যার পরশে দু-তীর ঘিরে সে গড়ে তুলেছে অপরূপ স্বপ্নদ্বীপ…ছোটো ছোটো গ্রাম। নদী আর খাল, শিমুল আর বকুল, বেত-বাতাবির ঝোঁপ-ঝাড় আরও কত অজস্র নাম জানা-না-জানা গাছ-গাছালির সবুজে শ্যামলে ঘেরা আমার এই ছেড়ে আসা গ্রাম খালিয়া।
আজ থেকে প্রায় চারশো বছর পূর্বে এক অপরাহু বেলা প্রায় শেষ হয় হয়। গোধূলির অন্তিম রক্তরাগ ছড়িয়ে পড়েছে কুমার নদীর প্রশান্ত জলধারায়। এমনি সময়ে তার তীরে এক প্রাচীন অশ্বত্থামূলে গভীর চিন্তামগ্ন এক তরুণ বসে বসে ভাবছে তার অনাগত বিধিলিপি। তার প্রশস্ত ললাটে পড়েছে গভীর চিন্তার সুস্পষ্ট রেখা। অনির্দেশ্য পথের উদ্ৰান্ত তরুণ যাত্রীর মনের একটি বন্ধ দুয়ার সহসা খুলে গেল। দূর-প্রান্তরের পানে তাকিয়ে চেয়ে থেকে দুঃসাহসিক অভিযাত্রী স্বগতোক্তি করল,–‘ওই প্রান্তরই হবে আমার প্রাচীন অশ্বথের আশ্রয়।’
বাংলার ইতিহাসের পাদটিকায় এই তরুণ ব্রাহ্মণ রাজারাম রায় নামে পরিচিত। রাজারাম আপনার বাহুবলে কালক্রমে ফরিদপুর জেলার এই কুমার নদীর তীরবর্তী বিস্তৃত অঞ্চলে একাধিপত্য বিস্তার করে খালিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর পাতার কুটির রূপ নিল সাতমহলা প্রাসাদে। তাঁর সেই বিশালায়তন প্রাসাদের এক-চতুর্থাংশ মাত্র আজ বর্তমান।
রাজারাম শুধু নিজের প্রাসাদ তৈরি করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, যেসব কারিগর, মজুর ও শিল্পীর অক্লান্ত শ্রম ও মমতায় তাঁর প্রাসাদটি গড়ে উঠেছিল, রাজারাম তাদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক, জমি, জায়গা প্রভৃতি দান করে নিজ গ্রামের পাশেই তাদের প্রতিষ্ঠিত করে দেন। এ ছাড়া রাজারাম তখনকার দিনে বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বংশের সুসন্তানদের এনে নিজ গৃহের আশপাশে তাদের বাড়ি-ঘর নির্মাণ করে দেন। ধীরে ধীরে রাজারামের প্রাসাদটিকে ঘিরে গড়ে উঠল একখানি ঐশ্বর্যশালী ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রাম।
কালক্রমে রাজারামের জমিদারি ও প্রতাপ এত দূর বিস্তৃত হয়েছিল যে, তদানীন্তন মোগল সম্রাট রাজারামকে রায় চতুর্ধারী উপাধিতে অলংকৃত করেন। ‘চতুর্ধারী’ শব্দের শব্দগত অর্থ হল যিনি চারিটি সেনাবাহিনীর অধিনায়ক। এই চতুর্ধারী শব্দই ক্রমে লোকমুখে রূপান্তরিত হয় চৌধুরিতে। কথিত আছে একবার বারোভূঁইয়াদের অন্যতম প্রধান সীতারাম রায় রাজারাম রায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু দোর্দন্ড প্রতাপ রাজারাম তাঁর অজেয় সেনাবাহিনীর সহায়তায় সীতারামকে পরাভূত করেন। এই অজেয় সেনাবাহিনীর অধিকাংশই ছিল নমঃশূদ্র প্রজাবৃন্দ। এরা একদিকে যেমন দুঃসাহসী ও দুর্দম, তেমনি সরল ও নম্র এদের প্রকৃতি। এরা প্রধানত জমির চাষ-আবাদ ও কুটির শিল্পের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। অনেকে করত মাঝি-মজুরের কাজ। আবার এরাই ছিল তখনকার দিনে প্রতাপশালী ভূস্বামীদের মজুত জঙ্গিবাহিনী।
কালের আবর্তনে সেই রাজারামের আমল অতীত হয়ে গিয়েছে কবে। তবু অলিখিত ইতিবৃত্ত ভাস্বর আখরে লেখা রয়েছে গাঁয়ের অন্তরের মণিকোঠায়। ছেলেবেলায় আমরা ঠাকুমা-দিদিমার মুখে রাজারাম রায়, জয়চন্দ্র রায়, তাঁদের পার্শ্বচর ভোলা বাগদি, রহিম শেখের রোমাঞ্চকর জীবন-কথা শুনে ভেবেছি–সত্যি কি তেমনি কাল কোনোদিন ছিল, না এ সবই কাল্পনিক রূপকথার কোনো অবাস্তব কাহিনি।
আড়াইশো বছরের ব্রিটিশ শাসন তার দুষ্টক্ষতের চিহ্ন যদিও রেখে গেছে পূর্ববাংলার প্রতিপল্লিতে, তবু সে আমলেও গ্রামগুলো যে কিছুটা উন্নত ও আধুনিক হয়েছিল সে-কথা অস্বীকার করব না। আমাদের খালিয়া গ্রামও কয়েকটি বিষয়ে আধুনিককালের সঙ্গে তাল রেখে চলেছিল। আমাদের বাড়ির পশ্চিম দিকে খালপাড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি ডাক ও টেলিগ্রাফ অফিস। আধুনিক সভ্যতার এক অমূল্য অবদান এই ডাক ও তার বিভাগ। সাতসমুদ্র তেরো নদী পারের আপন মানুষের নিরালা মনের কথা তারা এনে পৌঁছে দিয়েছে গাঁয়ের মানুষের কাছে। রোজ সকালে দেখতাম আমাদের গাঁয়ের ডাক-পিয়োন জলধর তার সেই চিরপরিচিত জীর্ণ ছাতাটি মাথায় দিয়ে একটা হলদে ক্যাম্বিসের ব্যাগ কাঁধে করে যখন বাজার খোলায় এসে হাজির হত তখন চারদিক থেকে গাঁয়ের লোকেরা তাকে অস্থির করে তুলত চিঠির তাগাদায়। যে বাষ্পীয় ইঞ্জিন একদিন সারাপাশ্চাত্য জগতের অগ্রগমনে দিয়েছিল অবিস্মরণীয় গতিবেগ–যার ঢেউ-এর দোলায় টেমস নদীর উপকূল থেকে প্রশান্ত মহাসাগর অবধি চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তার ক্ষীণ রেশ আমাদের এই আত্মভোলা কিশোরকুমার নদীর প্রশান্ত বুকেও এসে লেগেছিল। তাই দেখে এক সময় গাঁয়ের আবালবৃদ্ধবনিতা বিস্ময়ান্বিত হত। সেই প্রথম বিস্ময়ের পর অনেক দিন অতীত হয়ে গেছে, এখন আর গাঁয়ের লোকেরা জাহাজ দেখে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে না।
কত তন্দ্রাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় আকাশে উড়োজাহাজের ঝাঁক দেখে গাঁয়ের ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েরা মায়ের কোলে জড়োসড়ো হয়ে ডাগর চোখ দুটো তুলে বলত, ‘মা! ওই বুঝি সেই পরনকথার ব্যাঙ্গমা পাখি?’ গাঁয়ের শ্ৰীকণ্ঠ মুদি বলত, ও হল পুষ্পক রথ। কতদিন দেখেছি খালিয়া বাজারের পুলের কাছে শ্ৰীকণ্ঠ মুদির সেই দোকানটা হর ঠাকুরদার বক্তৃতায় সরগরম হয়ে উঠেছে। দেখেছি, হর ঠাকুরদা মাঝে মাঝে তাঁর হাত দু-খানা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রাইচরণ, নিতাই, রসুল মিয়াদের বোঝাচ্ছে,–‘বোঝলা কিনা রসুলভাই, সেই যে মহাভারতে ল্যাখছে পুষ্পক রথের কথা। হেই পুষ্পক রথই হেন উড়োহাঁস জাহাজ অইয়া আকাশে উইড়া বেড়ায়।’ শ্ৰীকণ্ঠও ঠাকুরদার কাছ থেকেই শুনেছে পুষ্পক রথের কাহিনি। রসুল নিরক্ষর চাষি। সে মহাভারত পড়েনি। তবু ওই শ্ৰীকণ্ঠ মুদির দোকানে বসেই সে মহাভারতের গল্প শুনেছে অনেকদিন। রসুল তার দাড়ির মধ্যে হাত বুলোতে বুলোতে বিজ্ঞের মতো কইত, ‘তা কথাডা ঠাউরমশায় যা কইছ হেথা একালে মিথ্যা নয়।’
গ্রামের বাজারে প্রতিবৎসর মেলা বসত চার বার! একটি বারুণীর দিনে, একটি পয়লা বৈশাখে, আর রথের সময় দু-দিন। পয়লা বৈশাখের মেলার নাম ‘গলুয়ের মেলা’। এইদিনে আগে কবিগান হত এবং অনেক দল পাল্লা দিয়ে গান করত। একবার একজন মেয়ে কবিওয়ালি প্রতিপক্ষকে বলেছিল,
ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখোনি কুনো,
মুখপোড়া গাবুর একটা বুনোনচ্ছার তোরে করব তুলোধুনো।
বলাবাহুল্য সকলের মতে তারই জিত হল।
আমাদের গাঁয়ের পূর্বপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত ছিল একটি প্রথম শ্রেণির উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়। রাজারামের নাম অনুসারেই গাঁয়ের লোকে তার নাম দিয়েছিল রাজারাম ইনস্টিটিউট। আশপাশের দু-দশখানা গাঁয়ের ছেলেরা এই শিক্ষায়তন থেকেই প্রবেশিকা উত্তীর্ণ হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে দেশে-বিদেশে। তাদের মধ্যে অনেকে আজ সমগ্র দেশের বরেণ্য সারাদেশের গৌরব। ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সভাপতি দেশবরেণ্য অম্বিকা মজুমদারমশায়ও একদিন এই রাজারাম ইনস্টিটিউটের ছাত্র ছিলেন। বাংলার অন্যতম প্রসিদ্ধ সাধক কবি ও দার্শনিক কিরণচন্দ্র দরবেশও ছিলেন এই খালিয়া গ্রামেরই ছেলে। তিনিও ছিলেন একদিন এই রাজারাম ইনস্টিটিউটের ছাত্র। বর্ষাকালে যখন খালিয়ার পথঘাট নদীনালা একাকার হয়ে যেত তখন আমাদের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণও জলে থইথই করত। ছাত্ররা তখন দূরদূরান্তর থেকে নৌকো করে এসে স্কুলে পড়াশোনা করত। যাদের নৌকো থাকত না তাদের ভোঙায় অথবা কলাগাছের ভেলায় করে স্কুলে আসতে হত। গাঁয়ের ছেলেদের মধ্যে লেখাপড়া শেখার আগ্রহ যে কত প্রবল ছিল এ থেকেই তার কিছুটা বোঝা যায়। এই বিদ্যালয়টির পেছনে ছিল অনাড়ম্বর শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম আর অকৃত্রিম অনুরাগ। কিন্তু আজ সে বিদ্যালয়টির চারদিক ঘিরে গুমরে উঠছে শুধু এক ‘নাই নাই’ রব। নাই সেসব নীরব দেশকর্মী শিক্ষকেরা–নাই সেসব দুষ্টুমি আর খুশিতে উজ্জ্বল কিশোর ছাত্রদের কলরব।
বিদ্যালয়টির পাশেই ছিল একটি সাধারণ গ্রন্থাগার। গাঁয়ের উৎসাহী তরুণ কর্মীরা এই গ্রন্থাগারটি গড়ে তুলেছিল।
স্বদেশি যুগে যেদিন বাংলার একপ্রান্ত থেকে আর-একপ্রান্ত অবধি বেজে উঠেছিল পরাধীনতার শিকল-ভাঙার ঝনঝনানি সেদিনও আমার এই ছেড়ে আসা গ্রামখানি সিংহের মতো অধীর হয়ে উঠেছিল শিকল ভাঙার উন্মাদনায়। বাবার কাছে শুনেছি কত নিস্তব্ধ অমারাত্রির অন্ধকারে খালিয়ার মুক্তিপাগল দুর্বিনীত তরুণদল তাদের স্বাধীনতার সাধনায় মগ্ন ছিল লোকচক্ষুর অগোচরে ঝোঁপ-জঙ্গল ঘেরা কালীমন্দিরের আঙিনায়! সেখানে চলত বিপ্লবীদের লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, বন্দুক চালনা, বোমা তৈরি, আর চলত গভীর মন্ত্রণা কী করে বেনিয়া দস্যু শ্বেতাঙ্গদের হটিয়ে দেওয়া যায় সাগরপারে। সারাভারতের বিপ্লবী বীর বালেশ্বর সংগ্রামের প্রথম শহিদ কিশোর চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরির সংগ্রামী জীবনের প্রথম অধ্যায় শুরু হয়েছিল এই খালিয়া গ্রামের ঝোপে-জঙ্গলে। যে স্বাধীনচেতা রাজারাম প্রাণের নিবিড় মমতায় গড়ে তুলেছিলেন এই খালিয়া গ্রাম-দেহের প্রতি রক্তবিন্দু দিয়ে রক্ষা করেছিলেন তার স্বাধীনতা, বহুযুগান্তে তারই এক বংশধর তরুণ বিপ্লবী চিত্তপ্রিয় সারাভারতের মুক্তির জন্যে বালেশ্বরের যজ্ঞভূমিতে নিজের অস্থিমজ্জা রক্তমাংস আহুতি দিয়ে পিতৃঋণ শোধ করে গেছে। জবাব দিয়েছে খালিয়া গ্রামের মুখপত্র সারাবাংলার হয়ে–সারাভারতের পক্ষ থেকে উদ্ধত শ্বেতাঙ্গ শাসনের ও শোষণের প্রতিবাদে। সেই শহিদ-তীর্থ খালিয়া গ্রামের মানুষ আজ ভারত শাসকদের কাছে উদবাস্তু মাত্র–আর কিছু নয়। কী মর্মান্তিক পরিহাস!
আজ আমার-ছেড়ে আসা গ্রামের কথা লিখতে বসে একটি দিনের কথা কেবলই মনে পড়ে। গ্রামে তখন শারদোৎসবের ধুমধাম। বহুদূরদেশ থেকে প্রবাসীরা সব গাঁয়ে ফিরে এসেছে মাটির মায়ের টানে। আমাদের গাঁয়ে প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই দুর্গোৎসব হয়ে থাকে। তাই পুজোর কটাদিন গাঁয়ের কারুরই থাকা-খাওয়ার কোনো বিধিনিয়ম থাকে না। সব বাড়িতেই সকলের নিমন্ত্রণ। ফেরার দিন সকাল থেকেই সব জিনিসপত্র বাঁধাছাদা শুরু হয়ে যায়। বিকেলেই বাড়ি থেকে যাত্রা করতে হবে। দিনটা দেখতে দেখতে কোথা দিয়ে গড়িয়ে গেল। বিকেল বেলায় দেখি রাজুদা বাইরের দাওয়ায় বসে গুড়ক গুড়ুক করে তামাক খাচ্ছে। মাথায় একটা লাল গামছা পাগড়ির মতো করে বাঁধা। রাজুদা আমাদের নৌকোর মাঝি। জাতে নমঃশূদ্র। আমাকে দেখেই রাজুদা বলে উঠল,–‘কি ছোটো-কর্তা, দেরি করতে আছ ক্যান। হ্যাঁসে তো ইস্টিমার পাব না য়্যানে। হকাল হকাল বাইরাইয়া পড়ো।’ বাড়ির দিঘির ঘাট থেকে যখন আমাদের নৌকা ছাড়ল তখন দিনের সূর্য ক্লান্ত হয়ে সন্ধের কোলে চলে পড়েছে। নৌকা যখন খালের প্রান্তে সাধুর বটতলার পাশ দিয়ে কুমার নদীতে পড়ল তখন গোধূলির স্বর্ণরেণু ছড়িয়ে পড়েছে আমার ছেড়ে আসা গ্রামখানির ওপরে। আমার ভাইবোনেরা নৌকার ছইয়ের ওপর বসে দেখছে সেই অপরূপ বিলীয়মান ছবি। গাঁয়ের সীমানা ছেড়ে যতই দূরে চলে আসছিলাম ততই আমার মন ব্যথাতুর হয়ে উঠেছিল কী এক অনির্দেশ্য বেদনায়। চোখ দুটো হয়ে উঠছিল অশ্রুছলছল। কী যেন নেই! কী যেন হারিয়েছি, কাকে যেন চাই, কাকে যেন আর পাব না– এমনি এক অসহায় মর্মরাঙা বেদনা আমার বুকের মধ্যে গুমরে উঠছিল। সেই অব্যক্ত বেদনার মূল আমি নিজেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না। শুধু অজ্ঞাতে অস্ফুটে কখন বলে চলেছিলাম,
মাতৃভূমি স্বর্গ নহে সে যে মাতৃভূমি,
তাই তার চক্ষে বহে অশ্রুজলধারা
যদি দু-দিনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দু-দন্ডের তরে।
গ্রাম ছেড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে পল্লিকবির রচিত একটি গান। লক্ষ্মণের শক্তিশেলে শ্রীরামচন্দ্র খেদোক্তি করে বলছেন,
সুমিত্রা মা বলবে যখন,
রাম এলি তুই কই রে লক্ষ্মণ–
(আমি) কোন প্রাণ ধরে বলব তখন :
মাগো, তোমার লক্ষ্মণ বেঁচে নাই।
দেশজোড়া লক্ষ্মণের দল আজ শক্তিশেলে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। কবে তাদের সবার মূৰ্ছা ভাঙবে সে আশায় দিন গুনছি।
.
চৌদ্দরশি
রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যে বাঁচতে চেয়েছিলেন এবং মানুষের মধ্যে বাঁচবার জন্যে প্রেরণার বাণীও দিয়ে গেছেন আমাদের। কিন্তু আমরা মানুষের কাছ থেকে নির্বাসিত হলাম, তাদের মধ্যে ঠাই তো পেলাম না! যেখানে আজীবন কাটালাম সেখানে আমাদের আর কোনো স্থান নেই আজ। কীর্তিনাশ ও যেখানে তার স্বভাবগুণে আমাদের বসবাসের জন্যে ‘চৌদ্দরশি’ জায়গাটি সৃষ্টি করল, সেখানে হিংস্র মানুষ আমাদের থাকতে না দিয়ে তার কুটিল অনুদার মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছে। কালবৈশাখীর হঠাৎ ঝড়ের তান্ডবে শীতের ঝরাপাতার মতো উড়ে গেলাম নিজের দেশ থেকে। এ ঝড় কোথা থেকে এল? কার অদৃশ্য কারসাজিতে আমাদের বাস্তুভিটে ছেড়ে আসতে হয়েছে? সমস্ত কিছু থাকা সত্ত্বেও কেন আজ আমরা ‘উদবাস্তু’ নামে চিহ্নিত হচ্ছি? একেই হয়তো অদৃষ্টের পরিহাস বলে! অঘটনপটন পাটোয়ারের দল যে তান্ডব সৃষ্টি করেছে তার ‘বলি’ আমরাই হলাম ভেবে মাঝে মাঝে চোখ জলে ঝাপসা হয়ে আসে।
আমাদের গ্রামের নাম চৌদ্দরশি। গ্রাম ছেড়ে এসেছি বটে, কিন্তু তার স্মৃতি ভুলতে পারছি কই? যেখানকার বাতাসে আমার সুখ-দুঃখ হাসি-কান্না মিশে রয়েছে তাকে এক কথায় মনের মণিকোঠা থেকে ঝেড়ে ফেলি কেমন করে? দৈহিক অপসরণ সম্ভব হলেও কল্পনার অশ্বমেধ ঘোড়াকে আটকাব কোন জাদু মন্ত্রে? এখনও অসতর্ক মুহূর্তে গ্রামের নদীর ধারের, বাবুদের ডাক্তারখানার, স্কুলের মাঠের, বাগানবাড়ির স্মৃতি রোমন্থনে ব্যস্ত হয়ে পড়ি। চৌদ্দরশি কি আজও প্রাণমাতানো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সকলকে আকর্ষণ করছে?
ফরিদপুর শহর থেকে চৌদ্দরশির দূরত্ব মাত্র পনেরো মাইল। বর্ষাকালে টেপাখোলা হয়ে নৌকোয় যেতে হয়, অন্য সময় মোটরে। ফরিদপুর জেলার সকলেই আমাদের গ্রামের নাম জানেন। জিজ্ঞাসা করলে সকলেই রাস্তা দেখিয়ে দিতে পারেন, যদিও মূল চৌদ্দরশি বলে কোনো নির্দিষ্ট গ্রামই নেই। পূর্বে স্থানটির বুকের ওপর দিয়ে বয়ে যেত কীর্তিনাশা পদ্মানদী। অকস্মাৎ তার গতিপথ বিপরীতগামী হওয়ায় তার বুকে প্রকান্ড চর জেগে ওঠে। যেখানে যখন চর জাগত জমিদারের লোক এসে মাপামাপি করত রশির ক্রমিক সংখ্যায়। এই চরগুলোই গ্রামের ভূমিকা। গ্রাম গড়ে ওঠে কীর্তিনাশার আনুকূল্যে, কিন্তু গ্রামের নাম থেকে যায় রশিমাপের সংখ্যাতত্ত্বের ওপরেই। এমনিভাবে পত্তন হয়েছে বাইশরশি, সাতরশি, নয়রশি ইত্যাদি নানা গ্রামের, আর এইসব গ্রামের সমষ্টিই শেষ পর্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছে চৌদ্দরশি ডাকনামে।
চৌদ্দরশি গ্রামের সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ছে গ্রামের জমিদারবাবুদের কথা। ‘জমিদার’ নামটির মধ্যে যে ভয়াবহতার চিহ্ন থাকে তা এঁদের মধ্যে ছিল না। এ জমিদারেরা অমায়িক। ফরিদপুর, বরিশাল, পাবনা জেলায় এঁদের বিরাট জমিদারি–এমন প্রতিপত্তিশীল জমিদার পূর্ববঙ্গে খুব কমই ছিল। তিন শরিকের জমিদারি, তিন ভাইয়ের তিন হিস্যে। তিনজনের বাড়ি, মন্দির, বাগান, দিঘি নিয়ে যেন তিনটি শহর। আমলা-কর্মচারী, পাইক-পেয়াদা, সেপাই, মোসায়েবের দল গিসগিস করত। বাবুরা পায়ে হেঁটে কোথাও বেরুতেন না, তাঁদের প্রত্যেকের ছিল সুসজ্জিত পালকি। পালকি-বেহারাদের হেঁইও হোহেঁইও হো-র একটানা শব্দ শুনেই বোঝা যেত কোন জমিদারবাবু আসছেন। পালকির সামনে পেছনে চলত বন্দুকধারী সেপাই। মনে পড়ছে বাবুদের দেখবার জন্যে গ্রামের ছেলে-বুড়ো এসে জুটত রাস্তার দু-পাশে। সে জনতায় হিন্দু-মুসলমান পৃথক হয়ে থাকত না,-গা ঘেঁষাঘেষি করে সবাই উঁকি দিত পালকির দরজায়। দেড়মাইল দূরে গ্রাম্যনদী ভুবনেশ্বরী। নদী চলার পথে জমা থাকত বাবুদের বড়ো বড়ো বজরা। আয়তনে ছিল মোটরলঞ্চের চেয়েও বড়। ত্রিশ চল্লিশ জন মাঝিমাল্লা ছাড়া এ বজরা চালানো সম্ভবপর হত না। মাঝিমাল্লারা ছিল প্রায় সকলেই মুসলমান। হিন্দু-জমিদারের সুখ-সুবিধের জন্যে তারা একদিন প্রাণ পর্যন্ত তুচ্ছ করতে পারত। গ্রাহ্যই করত না হিন্দু-মুসলমান ভেদাভেদের জিগিরকে। বাবুদের পেয়াদাও ছিল সকলেই মুসলমান তাদের লাঠি সড়কির ওপরেই নির্ভর করত বাবুদের মানসম্ভ্রম, প্রতিপত্তি, সেখানে কোনোদিন তো ভেদাভেদ দেখিনি। এক হিন্দু জমিদারের মুসলমান লাঠিয়ালরা বাবুর সম্মান রক্ষার জন্যে অন্য জমিদারের মুসলমান লাঠিয়ালের মাথা চূর্ণ করে এসেছে দ্বিধাহীন চিত্তে! ঠিক এর উলটোটাও হয়েছে। তখন মানুষ ছিল বড়ো। ধর্মের বিকৃতরূপ মানুষের মাথা খারাপ করতে পারেনি। মুসলমান পরিবারের সাহায্যার্থে কত হিন্দুকে নিঃস্বার্থভাবে দান করতে দেখেছি। বয়োজ্যেষ্ঠদের মুখে গোরুর গাড়ি বোঝাই করে টাকা পয়সা আসার গল্প শুনেছি। জমিদাররা ছিলেন এমনি ধনী। জাতিধর্ম নির্বিশেষে বহাল করতেন কর্মচারী। তাঁদের কাছে ধর্ম বড়ো ছিল না, বড়ো ছিল কর্মঠ লোকের অকৃত্রিম পরিশ্রম। মুসলমানরাও বুঝত সে কথা, তাই তাদের কাজে কোথাও ফাঁকি থাকত না। বড়ো হিস্যের রায়বাহাদুর মহেন্দ্রনারায়ণ, মেজো হিস্যের রমেশচন্দ্র ও ছোটো হিস্যের দক্ষিণারঞ্জন ছিলেন প্রসিদ্ধ। তাঁদের জমিদারি তদারকের জন্যে থাকত তিনজন অবসরপ্রাপ্ত জজ বা ম্যাজিস্ট্রেট।
হিন্দু হলেও তিন শরিকের মধ্যে কখনো কখনো বিবাদ বাধত, কিন্তু সে কলহের ফল সাধারণত হত শুভই। জনসাধারণ তাঁদের কলহমন্থন করে লাভ করত অমৃত। বড়োবাবু নিজের সুনামবৃদ্ধির জন্যে যেই দুটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন, মেজোবাবু তার পালটা জবাব দিলেন ফরিদপুরে রাজেন্দ্র কলেজ বসিয়ে। ছোটোবাবু চুপ করে থাকতে পারেন না। ফরিদপুরে উদবোধন করলেন সিনেমা হাউসের। এমনিভাবে সুস্থ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে জনগণ পেল হাই স্কুল, হাসপাতাল, কলেজ ইত্যাদি। এগুলো থেকে সুযোগ-সুবিধে পেত গ্রামবাসীরাই। হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টানের গন্ডি টেনে কোনোদিন এসব প্রতিষ্ঠানকে খাটো করা হয়নি। আজ আর সেদিন নেই।
গ্রামে দুর্গা পুজোকে কেন্দ্র করেই সবচেয়ে বড়ো আনন্দোৎসবের ব্যবস্থা হত। সবচেয়ে ধুম হত জমিদারবাড়িতে। গ্রামবাসীরা যে যেখানেই থাক, এসে জমায়েত হত এই সময়টিতে। কয়েকদিনের জন্যে গ্রামের বুকে অপূর্ব হিল্লোল জাগত যেন। পুজোর তোড়জোড় চলত একমাস আগে থেকে। এই উপলক্ষ্যে ময়দান ভরে যেত রকমারি দোকানপাতিতে, কার্নিভাল ও সার্কাসে। আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে ভরে যেত দেশ। এই আনন্দের পূর্ণাহুতি হত তখন যখন কলকাতা থেকে আসত নামকরা যাত্রার দল। আজ আর যাত্রাগানের আদর নেই তার এই উৎসভূমি কলকাতায়। কিন্তু মনে পড়ে দেশে আমরা যাত্রা শোনবার জন্যে কত রাত্রি পর্যন্ত উৎসুক হয়ে কাটিয়েছি। কত রাত্রি অনিদ্রায় কেটে গেছে কোন দল আসছে তারই জল্পনা-কল্পনায়! কোন দলের কোন অভিনেতা অন্যদলের চেয়ে ভালো তা নিয়ে হাতাহাতি পর্যন্ত হয়ে গেছে ভেবে আজ এত দুঃখের মধ্যেও হাসি আসে! যাত্রাগান শোনার জন্যে শ্রোতারা আসত দূরান্তরের গ্রাম থেকে। বিদেশ থেকে আসত আত্মীয় পরিজনবর্গ। অপূর্ব আনন্দ কোলাহলে দিনগুলো কোথা দিয়ে যে চলে যেত বোঝাই যেত না। টনক নড়ত গ্রাম ছাড়বার সময়। সাময়িকভাবে গ্রাম ছাড়তেও যাদের চোখে জল আসত সেদিন, আজ তারা চিরতরে কী করে গ্রাম ছেড়ে দিন কাটাচ্ছে?
মনে পড়ে বাড়ির বাঁধানো পুকুরঘাটে, বাগানের মধ্যে কত আশাময় ভবিষ্যৎ সুখস্বপ্নের কথা হয়েছে। পুজোর একসপ্তাহ আগে থেকে রাতের পর রাত জেগে হয়েছে গান শোনা এবং গাওয়ার তীব্র প্রতিযোগিতা। নবমীর মোষ বলি দেখে কত ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়ে ভয় পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কোলে চোখ বুজে রয়েছে। পশুরক্ত দেখে মুসলমানকে আতঙ্কিত হতে দেখেছি সেদিন। কিন্তু আজ কাদের প্ররোচনায় মানুষের রক্তও মানুষের মনে বিতৃষ্ণা আনতে পারছে না? অসভ্য পার্বত্য জাতির মধ্যে আজও নরবলি হয়ে থাকে শুনি। কিন্তু বাংলা তথা ভারতবর্ষের বুকের ওপর দিয়ে ওই যে নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়ে গেল, তা যেন সেইসব বর্বর জাতিকেও লজ্জা দেয়।
আমাদের স্কুলটি ছিল বড়ো চমৎকার। সামনে খোলা মাঠ, পেছনে শ্রেণিবদ্ধ আমবাগান। মাঝখানে বাঁধানো পুকুর। ছবির মত পরিবেশ। আমাদের মাস্টারমশায় সুরেশবাবু ছিলেন সেই স্কুলের প্রাণ। পড়াশোনায়, খেলাধুলায় তিনি অনুপস্থিত থাকলে পন্ড হয়ে যেত সব কিছুই। আজ বহু কর্মীপুরুষের সান্নিধ্যে এসেও তাঁর কর্মনিষ্ঠার মনোমুগ্ধকর ছবি বড়ো হয়ে চোখের সামনে ভাসছে দিনরাত। তাঁরই উৎসাহে আমাদের “Rashi’s Eleven Football Club”-এর জন্ম হয়েছিল! ফুটবল খেলার জন্যে আমরা তখন পাগল,–ফুটবলের জন্যে রাজ্যপাট বিলিয়ে দিতেও তখন আমরা পেছপা নই! রাম, মালি, লক্ষ্মণ, বিশু, ব্ৰজা, নৃপেন আর সুরেশবাবুকে নিয়ে আমরা পনেরো-বিশ মাইল পথ পাড়ি জমাতাম ম্যাচ খেলার জন্যে। কোনো বাধাই আমাদের আটকে রাখতে পারত না।
ডাক্তারখানার পুকুরঘাটে ছিল আমাদের আড্ডাখানা। বিকেল হতে-না-হতেই এসে জমায়েত হতাম সেখানে। জার্মানির ফ্যাসিবাদ নিয়ে, চার্চিলের ইম্পিরিয়ালিজম নিয়ে, আমেরিকার অ্যাটম বম নিয়ে, আজাদ হিন্দ ফৌজের সৈন্য নিয়ে আমাদের তর্কের শেষ থাকত না। এ আড্ডায় হিন্দু-মুসলমানের অবাধ গতায়াত ছিল। শান্তির সপক্ষে উভয় সম্প্রদায়ই ছিল সমান উৎসুক। কিন্তু শান্তির জন্যে যেসব যুক্তিজালের অবতারণা হত সেদিন, আজ আঘাত পেয়ে বুঝেছি তা ছিল ভুয়ো! মুখে শান্তির বুলি আউড়ে মনে সংগ্রামের বিষ জিইয়ে রেখে মানুষ আর যাই করুক দেশের দশের মঙ্গল সাধন করতে পারবে না কোনোদিন। মানবতাবোধের অপমান সমগ্র মানবজাতিকেই হাড়ে হাড়ে পঙ্গু করে দেবে একদিন।
চৌদ্দরশির বাজার আমাদের তল্লাটের নামকরা বাজার। মঙ্গলবার ও শনিবারে হাট বসার জন্যে বহুদূর গ্রামাঞ্চল থেকেও লোক আসত বেচাকেনার জন্যে। ধান, চাল, পাট, দুধ, মাছ, তরিতরকারির রাশি রাশি অস্পষ্ট ছবি আজ মনে পড়লে স্বপ্ন বলে ভুল হয়। অল্প মূল্যে বেশি জিনিস এখানে কোথায় পাওয়া যাবে বলুন? ‘দুধ বা মাছ’ কোনোদিন আমাদের গ্রামে সের হিসেবে বিক্রি হয়নি। খুব মাগগি বাজারেও চার আনায় আড়াই সের খাঁটি দুধের হাঁড়ি কিনেছি। তরিতরকারি তো নামমাত্র মূল্য।
বুধাই শীলকে মনে পড়ে। ‘বুদ্ধিদা’ বলে আমরা ডাকতাম তাঁকে। সংগীতবিদ্যায় তাঁর কৃতিত্ব স্মরণযোগ্য। তবলা, হারমোনিয়াম, সেতার যন্ত্রে তাঁর হাত ছিল অসাধারণ। তাঁর আঙুলের স্পর্শ পেয়ে বাদ্যযন্ত্রগুলো যেন কথা বলে উঠেছে। আমরা ছিলাম তাঁর বাজনার নিয়মিত শ্রোতা। বাবুদের বাড়িতে গানবাজনার আসর বসলেই বুদ্ধিদার ডাক পড়ত সকলের আগে। ওঁদের বাড়িতে শিক্ষকতা করে তাঁর সংসার নির্বাহ হত। আজ বুদ্ধিদা কোথায়? সংহারের উন্মত্ত পরিবেশের মধ্যে সংগীতের সৃজনী প্রতিভা কোনো নিরাপদ দূরত্বে তাঁকে নিয়ে যেতে পেরেছে কি না জানি না! দূরে গিয়েও তিনি বেঁচে আছেন কি না তাই বা কে বলে দেবে? ডাক্তারখানার পুকুরে আজ আর লোকসমাগম হয় না শুনেছি। স্কুলের মাঠের আর সে পরিবেশ নেই, সুরেশবাবুও অন্য কোথাও পলাতক, পূজাবকাশে জনতার ভিড় নেই, জমিদারবাড়িতেও পুজো বন্ধ। সব আনন্দ কে যেন একসঙ্গে অপহরণ করে নিয়ে এক অভিশপ্তভূমিতে রূপান্তরিত করে দিয়েছে সমস্ত দেশটিকে। আমরা আজ আপন ঘরেই তাই পরবাসী।
.
খাসকান্দি
অনেকদিন আগেকার কথা।
চাকরি উপলক্ষে কিছুদিন ছিলাম অসমের, এক মহকুমা-শহরে। আত্মীয়স্বজনবিহীন প্রবাসজীবনে তখন আসন্ন ছুটির মধুর আমেজ। সকালে সবে ঘুম থেকে উঠেছি। এমনসময় দেখা দিলেন এক নব-পরিচিত বন্ধু। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুতে উঠলাম। দেয়ালে পেরেক ঠুকে সাজানো ছিল একগাদা টুকরো কাগজ। তাতে টুথ-পাউডার ঢেলে নেওয়া রোজকার অভ্যেস। সেদিনও ছিঁড়ে নিলাম একটুকরো কাগজ। আপন মনেই বললাম : আর একুশ দিন।
বন্ধু শুধালেন : কীসের একুশ দিন?
হেসে বললাম : ছুটির বাকি।
পেরেক ঠোকা কাগজগুলোর দিকে চেয়ে বন্ধু শুধোলেন : তাই কি ওতে লিখে রেখেছেন একুশ?
আজ্ঞে হ্যাঁ। শুধু একুশ নয়, পর পর লেখা আছে এক পর্যন্ত।
বন্ধু বিস্মিত হলেন : কেন বলুন তো?
কারণ একটা দিন যায় আর ভেবে আনন্দ পাই যে, ছুটিটা আরও একটা দিন এগিয়ে এল। ওঃ, ছুটিতে বাড়ি যাবার জন্যে আপনি তো একেবারে পাগল দেখছি!
সবিনয়ে জবাব দিলাম : শুধু বাড়ি যাবার জন্যে নয়, পাগল হয়ে আছি গাঁয়ে যাবার জন্যে ।
বলেন কী, এই বয়সেও গাঁয়ের জন্যে আপনার এত মমতা? গাঁয়ের মাটির জন্যে এত তীব্র আকর্ষণ।
নিশ্চয়ই! তাই তো কবি দেবেন সেন বলেছেন,
সব তীর্থ সার
তাই মা তোমার কাছে এসেছি আবার।
আরও অনেক কথাই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সেদিন বলেছিলাম। বন্ধু একটুখানি হেসেছিলেন মাত্র।
আমিও হেসেছিলাম সেদিন রাতে। জাগরণে নয়, স্বপ্নে।
ধুলো-ঢাকা যশোর রোডের বুকে নেমেছে বৈশাখী পূর্ণিমার উজ্জ্বল জ্যোছনা। পথের দু ধারে অর্জুন গাছগুলো দাঁড়িয়ে আছে নিস্তব্ধ প্রহরীর মতো। আলো-ছায়ার আলপনা আঁকা পড়েছে ধুলোর রাস্তায়।
ওই তো দেখা যায় বাঁশতলার পুল। বর্ষার খরস্রোত কুমারের উদ্ধত জলধারা যখন ওই সংকীর্ণ পুলের সংকীর্ণতর ছিদ্রপথে পথ খুঁজে মাথা আছড়াত অবিশ্রাম, পুলের মুখে তখন প্রতিবৎসর সৃষ্টি হত একটা তীব্র ঘূর্ণাবর্ত। ছেলেবেলায় আমরা ওকে বলতাম ‘বাটি’। ক্ষুধার্ত কুমার-নন্দন যেন মুখর মুখব্যাদান করে আছে তীব্র আক্রোশে। ছেলেবেলায় আমরা পুলের ওপর থেকে ওর ক্ষুধার্ত মুখে ফেলে দেখতাম কচুর পাতা, বটের ছোটো ডাল, ভাঁট ফুল, আরও কত কী। সেগুলো স্রোতের মুখে দু-তিনটে পাক খেয়ে ঘূর্ণাবর্তের অতল গহ্বরে যেত তলিয়ে। আমরা উচ্ছ্বসিত আনন্দে হেসে উঠতাম করতালি দিয়ে। ঘটনার ক্ষুরধার ঘূর্ণাবর্তে আজও অতলে তলিয়ে যাচ্ছে জীবনের আশা, আনন্দ, করতালি। কিন্তু আজ আর হাসবার অবসর নেই। আজ শুধু ক্রন্দন। কুমার, পদ্মা, মেঘনার তীরে তীরে শুধুই মর্মভেদী হাহাকার।
কিন্তু যে-কথা বলছিলাম।
ওই বাঁশতলার পুলের পাশ দিয়ে জেলা বোর্ডের ছোটো রাস্তা। দু-পাশ ধরে ছোটো ছোটো খেজুর গাছের সারি। ধানের খেত। দিগন্তবিস্তৃত গজারের বিলের রহস্যময় হাতছানি।
রাস্তা ধরে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলেই ছোটো কাঠের একটা পুল। মস্ত বড় একটা তেঁতুল গাছের ছায়া দিয়ে ঘেরা। পুলের দু-পাশ দিয়ে কাঠের রেলিং! সকাল-সন্ধ্যায়, সময়ে অসময়ে গ্রামের ছেলে-বুড়ো সকলের ওটা বেওয়ারিশ আড্ডার জায়গা। বর্ষায় ওর আশপাশে ছোটো ছোটো ছিপ দিয়ে মাছ ধরে ছোটো ছোটো ছেলেরা। বসন্ত সন্ধ্যায় ওই রেলিংয়ে ভর দিয়ে গলা ছেড়ে গান গায় কিশোর বালকের দল। যুবকদের আড্ডা-ইয়ার্কি চলে রাতের প্রথম প্রহর পর্যন্ত। ক্রমে রাত বাড়তে থাকে। ঝিঁঝি পোকার একটানা ডাকে মন্থর হয়ে আসে পল্লির আকাশ। বৃদ্ধেরা তখন ওই পুলে জমায়েত হয় সমাজ পঞ্চায়েতের ভূমিকা নিয়ে। ন্যায় ও অন্যায় শাসনের রকমারি ফতোয়া জারি করে। পুলের নীচে খালের জলধারা কুলকুল রবে বয়ে চলে।
এই তো পৌঁছে গেলাম গাঁয়ে।
গ্রাম, কিন্তু ম্যালেরিয়া-বিধ্বস্ত, নিরানন্দ, কুঁড়েঘর সম্বল কতকগুলো জীর্ণ শীর্ণ স্বপ্নহীন মানুষের বাসভূমি নয়। ঝকঝকে টিনের দু-তিন মহলা বাড়ি, আম-জাম নারিকেল-সুপারি কাঁঠালের বাগান, তাল-খেজুর গাছের গুঁড়ি দিয়ে ঘাট বাঁধানো কাক-চক্ষু জলভরা পুকুর, ত্রিনাথ-বাউল-হরিকীর্তন-যাত্রাদলের আনন্দধ্বনি মুখরিত প্রাঙ্গণ, আর পর্যাপ্ত আহার-নিদ্রা লালিত-তৈলচিক্কণ মানুষ–এই নিয়ে গড়া একটি মানববসতি। এই বাংলার গ্রাম। তোমার আমার সকলের। হায় রে সেদিন!
গ্রামে ঢুকতেই বাঁ-দিকে আগাছায় ঢাকা একটি পোড়ো ভিটে। গ্রামের ছেলে-বুড়ো যাকেই পরিচয় জিজ্ঞাসা করো, বলবে–হরিকাকার ভিটে।
ক্ষণেকের তরে সময়ের নদীতে লাগুক উজানের টান। ফিরে চলো কুড়ি বছর আগেকার এক মধুর চৈত্রসন্ধ্যায়।
হরিকাকার বাড়ি। সামনে আমগাছে ঘেরা বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের একপাশে চৈত্র পুজোর আসন পাতা।
দাওয়ায় বসে আছেন হরিকাকা। গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের সরকারি কাকা। একহারা কালো চেহারা, করিৎকর্মা লোক। গ্রামের যাত্রাদলে পার্ট করেন। অর্জুনের ভূমিকা থেকে ঘেসড়ার ঘুঙুর-নৃত্য অবধি সব অভিনয়ে তিনি সমান দক্ষ।
হরিকাকা এবার জুড়ে দিয়েছেন চৈত্র পুজোর মেলা।
বিকেল হতেই গাঁয়ের শৌখিন ছেলে-বুড়োর দল একে একে জমতে লাগল কাকার আঙিনায়। আম গাছের তলায় কলার পাতা পেতে সবাই এক সঙ্গে পেল খিচুড়ি প্রসাদ। তারপর সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হল বেলোয়ারি সং নিয়ে গ্রাম প্রদক্ষিণ। কেউ সাজল লোলজিহ্বা খঙ্গহস্ত মহাকালী, কেউ-বা বাঁশরিভূষণ শ্রীনন্দন কেউ ত্রিশূলধারী শ্মশানচারী ভোলানাথ, আবার কেউ-বা নৃত্যপরায়ণা সুন্দরী উর্বশী।
সারারাত ধরে চলে গৃহ হতে গৃহান্তরে সং নিয়ে পল্লিপরিক্রমা। পল্লিবাসীরা পরম আগ্রহে সঙের দলকে বাড়িতে ডেকে নেয়। গান শোনে। নাচ দেখে। সাধ্যমতো ‘বিদায়ি’ দেয় চাল ডাল পয়সা। দেখতে দেখতে সঙের দলের ভান্ডারীর ঝুলি ভরে ওঠে। কালের কুটিল গতি! সেই পল্লীবাসীরা আজ কোথায়?
অতএব ওপথ ছেড়ে চলো যাই গ্রামের ‘তরুণ পাঠাগারে। ওপাড়ার মুখুজ্জেদের কাছারি বাড়িতে গাঁয়ের ছেলেদের নিজের হাতে গড়া পাবলিক লাইব্রেরি। অনেকরকম বই ওখানে পাবে। গণেশ দেউস্করের দেশের কথা থেকে পাঁচকড়ি দে-র নীলবসনা সুন্দরী পর্যন্ত। পড়তে পড়তে সবুজ সঙ্ঘের মুখপত্র হাতে-লেখা মাসিক পত্রিকা ‘তরু’-র কয়েকটি পুরোনো সংখ্যাও হয়তো পেয়ে যাবে। তাতে কত সম্ভব অসম্ভব ধরনের লেখার সন্ধান পাবে তা তুমি কল্পনাও করতে পারো না। দেশ-উদ্ধারের এক বিষম জ্বালাময়ী পরিকল্পনার যে আভাস ওতে প্রকাশিত হয়েছিল তার সন্ধানে একদিন পরমপরাক্রমশালী ব্রিটিশ শক্তির পর্যন্ত টনক নড়ে উঠেছিল। হাসবার কথা নয়। সত্যি, ওই পাঠাগারে অনেকবার পুলিশ সার্চ করেছে। কিন্তু সার্চের দিন আজ গত হয়েছে। ওই পাঠাগারের পাশের রাস্তা দিয়ে এখন ‘মার্চ’ করে চলেছে নতুন কালের পুলিশ। জানি না সে মার্চ কোনো ফার্স’ হয়ে দাঁড়াবে কি না। সেখানকার একালের অধিবাসীরা আজ গৃহহারা বাস্তুত্যাগী। তাদের হাতে ভিক্ষার ঝুলি।
কিন্তু গ্রাম পরিক্রমার এখনও অনেক বাকি। হরিকাকার বাড়ি বাঁয়ে রেখে, ডাইনে ফেলে অশ্বত্থা-গজানো উঁচু দোলমঞ্চ-চলো আরও এগিয়ে!
উলুধ্বনি শুনতে পাচ্ছ? বেলা এখন দুপুর। গাঁয়ের কোনো সম্ভ্রান্ত সীমান্তিনী বুঝি ‘দুধ-চিনি’ দিতে এসেছে পুজোমন্ডপে। কবে হয়তো ছেলের জ্বর হয়েছিল গরম লেগে। স্নেহময়ী মাতা মানত করেছিল পুত্রের রোগমুক্তি হলে পুজোমন্ডপে দেবীর আসনে দেবে দুধ-চিনি। ও তারই কণ্ঠের উলুধ্বনি। তুমি যদি এখন সেখানে উপনীত হও, তাহলেও প্রসাদ পাবে একটু চিনি বা একটুকরো বাতাসা। পল্লির দেবসেবার সঙ্গে মানব-সেবার যোগ অঙ্গাঙ্গি।
ওই পুজোমন্ডপে এ গাঁয়ের ‘টাউন হল’, আশপাশের পাঁচ গাঁয়ের ফৌজদারি দেওয়ানি আদালত। বছরে একবার এখানে হয় মহিষমর্দিনী দুর্গাপুজো। গাঁয়ের ছেলে-বুড়ো সকলের মন পুজোর তিনদিন বাঁধা থাকে এই মন্ডপের চতু:সীমানায়। গান বলল, বাজনা বল, আনন্দ বল, উৎসব বল,–সারাগাঁয়ের উচ্ছ্বসিত আনন্দ-ধারা ওকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। ওই পুজোমন্ডপ গ্রামের প্রাণকেন্দ্র। সন্ধ্যায় ওখানে গ্রামবৃদ্ধ সমাজপতিদের সভা বসে। কত আলাপ-আলোচনা, বিচারদন্ড চলে। প্রতিরবিবারে বসে হরি-সংকীর্তনের আসর। কলিযুগের মুক্তিমন্ত্র হরিনাম আর মৃদঙ্গের বোলে নৈশ পল্লির তারাভরা আকাশ মুখর হয়ে ওঠে। হায় রে! বাংলার সে-আকাশ জুড়ে আজ সর্বহারা আর্তনাদ, মৃত্যুর বীভৎস হাহাকার।
ওই পথ ধরে আরও খানিকটা এগিয়ে গেলেই দেখতে পাবে টিনের আটচালায় বসেছে পাঠশালা। কানাই মাস্টার রজব মৌলবির শিক্ষাদান চলেছে অব্যাহত গতিতে। পাঠশালার সামনে দেখবে, ছেলেরা সার ধরে দাঁড়িয়ে নামতা পড়ছে সমবেত কণ্ঠে–দুই একে দুই, দুই দু-গুনে চার ইত্যাদি।
তাই বলে এই ভরা দুপুরবেলা ওপথ ধরে আর যেয়ো না কিন্তু। জানো না তো আর কিছুটা এগিয়েই পথ শেষ হয়েছে পুরোনো কালীখোলায়। বেতের ঝোঁপ আর ভাটির জঙ্গল দিয়ে ঘেরা সামান্য একটু জায়গা। দুটো প্রাচীন বট গাছ শাখা-প্রশাখা মেলে জায়গাটা একেবারে ঢেকে রেখেছে। তারি একপাশে খড়ের ভাঙা মন্দিরে বিকট দর্শন বিরাট কালীমূর্তি। উইয়ের ঢিপিতে ঢেকে গেছে পদতলে শায়িত মহাদেবের অর্ধেক দেহ। কাটা-কুমড়োর লতা এসে ঘিরে ধরেছে কালামূর্তির রূপালি মুকুট। একপাশে হয় তো আস্তানা গেড়েছে শেয়াল। ও নাকি মা কালীর জাগ্রত রক্ষী। তোমাকে দেখে যদি হঠাৎ ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে চেঁচিয়ে ওঠে, তবে আর রক্ষা নেই। মা কালীর তৃতীয় নয়ন নাকি তাহলে বিদ্যুৎ চমকের মতো একবার তোমার ওপর দিয়ে খেলে যাবে। আর অমনি তুমি বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে–
আর কোথায় যাও? এই তো গ্রামের শেষ। ওই তো সামনে ধু-ধু করছে চম্পার বিল। তার থই থই-করা কালো জলে লাল পদ্মফুলের আলোকরা শোভা। সেই পদ্মফুল একদিন দিয়েছিলাম কিশোরবেলায় বন্ধুর হাতে অনুরাগের লীলাকমল করে। ফুল পেয়ে কিশোর বন্ধু উচ্ছ্বসিত হয়ে আমায় প্রণাম করেছিল। তার ছেলেমানুষিতে আমি হেসে উঠেছিলাম অট্টহাসি। সেই হাসি হেসেছিলাম আর-একদিন অসমের এক মহকুমা-শহরে। জাগরণে নয়, লীলাকমলের স্বপ্ন দেখে।
কিন্তু যে স্বপ্ন এতক্ষণ তোমায় দেখালাম, সে তো শুধুই স্বপ্ন নয়। একদিন তো এই-ই সত্য ছিল। যে গ্রামটিকে কেন্দ্র করে একদিন স্বপ্নের জাল বুনেছিল অনেক কিশোরমানুষ সে তো একটি গ্রামমাত্র নয়, সে যে গ্রামকেন্দ্রিক বাঙালি সভ্যতার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।
গ্রামের নাম খাসকান্দি। ফরিদপুরের জেলা শহর থেকে যশোর রোড ধরে মাত্র সাত মাইল দুরে একটি সম্পন্ন-গ্রাম। সকাল বেলাকার নগর-সংকীর্তনের দল, দুপুরের পাঠশালা, অপরাহুের দুধের বাজার আর রাতের যাত্রাদলের আসরের জন্যে আশপাশের অনেক মানুষের মুখে মুখে একদিন ফিরত এই গ্রামের প্রশংসাধ্বনি। কিন্তু সে গ্রামের কথা আজ বুঝি আবাস্তব স্বপন-কাহিনিতেই পর্যবসিত হয়। হায় রে ধূলিলুষ্ঠিত বিশুষ্ক পলাশ, লীলাকমল! হায় রে আমার সোনার গ্রাম–আমার ছেড়ে-আসা গ্রাম!
.
কুলপদ্দি
ছোটোবেলার দিদিমার কোলে বসে এক স্বপনপুরীর গল্প শুনতাম। সেখানে গাছে গাছে সোনা ফলত। হিরার মতো বৃষ্টিরা ঝাঁক বেঁধে নেমে আসত সেই দেশের বুকে। নদীর কলতানে শোনা যেত বীণার ঝংকার। কত আগ্রহ নিয়ে সেই দিন সেই গল্প শুনেছি আর প্রশ্নের পর প্রশ্নে বিরক্ত করে তুলেছি বৃদ্ধা দিদিমাকে। সেদিন কি একবারও ভেবেছি যে আমাকেও একদিন এমনি গল্প শোনাতে হবে সকলকে; মাত্র ত্রিশ বছর বয়সেই পঙ্গু মন নিয়ে দিদিমার অভিনয় করতে হবে সারাটা দেশের সামনে?
দিদিমা মারা গিয়েছেন অনেককাল, কিন্তু অক্ষয় হয়ে আছে সেই স্বপনপুরী। সেদিনকার অবুঝ মনে সহানুভূতি জাগ্রত বন্দিনি রাজকন্যার জন্যে, আজ নিজের দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে নিজের ওপরই অনুকম্পা হয়। তাই মনে মনে এখন স্বপ্নের জাল বুনি, স্মৃতির কুসুম নিয়ে রচনা করি তারই কাহিনি, কবিরা কল্পনায় যাকে গড়ে তোলে কাব্যে, আজন্ম শহরবাসীরা যার ছবি দেখে স্বপ্নে।
আড়িয়ালখাঁ নদী নয় নদ। স্ত্রী নয়, পুরুষ। কিন্তু তাকে পুরুষ কল্পনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। শুধু আমি কেন, তরঙ্গভঙ্গে উজ্জ্বল আড়িয়ালখাঁর তীরে দাঁড়িয়ে জগতের সবচেয়ে বেরসিক লোকও বোধ হয় বলতে পারে না- খাঁ সাহেব এমন নেচে নেচে কোথায় যাচ্ছ তুমি? তবু আড়িয়ালখাঁ নদী নয়, নদ। তার নাম গঙ্গা বা যমুনার মতো কিছুই হতে পারবে না, তার নাম থাকবে–আড়িয়ালখাঁ।
এই আড়িয়ালখাঁর তীরে আমার গ্রাম–কুলপদ্দি। দেশের কুলপঞ্জিতে এর জন্মতারিখের সন্ধান পাওয়া যায়নি, তাই নামকরণের ইতিহাসটিও জানানো গেল না; তবে গাঁয়ের বহুপুরোনো স্মৃতি পুরোনো বন্ধুর মতোই মনের পর্দায় জড়িয়ে জড়িয়ে রয়েছে।
প্রকান্ড গ্রাম। প্রায় পাঁচ হাজার অধিবাসীর সুখ-দুঃখের কাহিনি দিয়ে এর ইতিহাস গড়া আর ভৌগোলিক সীমারেখার সঠিক পরিচয় পাওয়া যায় মাদারিপুর মিউনিসিপ্যালিটির বাঁধানো খাতায়। পৌর-প্রতিষ্ঠানের অঙ্গীভূত গ্রাম। তাই আশপাশের গ্রামগুলোর কাছে সে ভোজসভায় নৈকষ্যকুলীনের মতো, দেবসভায় ইন্দ্রতুল্য। যদিও বিদ্যাসাগরের মতো কেউ জন্মাননি আমাদের গ্রামে, কোনো বাদশাহি আমলের ইমামবাড়াও নেই এর ত্রিসীমানায়, তবু সেজন্যে কোনো দুঃখ নেই আমাদের। সেখানে যা আছে তাই যথেষ্ট-শালুকভরা বিল, গাছে গাছে পোষ-না মানা পাখি, ধু-ধু করা মাঠে সোনার ফসল।
কতদিন নির্জন মাঠে শুয়ে শুয়ে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করেছি। মনে হত এই গাঁয়ের একজন বলেই হয়তো চাঁদের আলো ঠিকরে পড়ত আমার ঘরে! শরতের বাতাস উতলা হয়ে উঠত শেফালি ফুলের গন্ধে। বৈশাখের অপরাহ্বে যেখানে গাঁয়ের ছেলেরা ফুটবল খেলত আনন্দের প্রস্রবণ বইয়ে দিয়ে, বর্ষার ভরা বাদলে সেখানেই ডিঙি নিয়ে আসত ভিন গাঁয়ের লোকেরা বাজারে সওদা করতে। জ্যোৎস্না রাতে বড়ো গাঙের মাঝি জোর গলায় গান ধরত—’মরমিয়া রে, ও মরমিয়া। মোর মনের কথা কইমু আজি তোরে।’ সেই পল্লিগীতির সুরটুকু এখনও আমার মনে লেগে রয়েছে, শহরের কোলাহলে আজও তা মুছে যায়নি।
নাগমশাই ছিলেন পাঠলারার শিক্ষক। ছোটোখাটো লোকটি বয়সে নয়, আকৃতিতে। তাঁর বেতখানির কথা মনে পড়ে। সুদীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে স্ত্রী সুনন্দা এবং ওই বেত্রদন্ডখানা তাঁর সুখ-দুঃখের সঙ্গী। ওই বেতখানা দেখিয়ে দেখিয়ে সেদিন তিনি ছাত্র পড়াতেন। আজ সে-স্কুল ভেঙে গিয়েছে, ঘটনার আকস্মিকতায় স্তব্ধ হয়ে যেন দাঁড়িয়ে পড়েছে নাগমশায়ের গতানুগতিকতা।
কেশবদাকে ভুলিনি। কী দুর্দান্ত প্রতাপ ছিল তাঁর যুবামহলে! গাঁয়ের এমন একটি ছেলেও ছিল না যে কেশবদার কথার অবাধ্য হতে সাহস পেত। সময়টা ছিল অগ্নিযুগ। আমি স্কুলে পড়ি। একদিন দুপুর বেলা স্কুল হতে ফিরছি, হঠাৎ কেশবদার সঙ্গে দেখা,–এই শোন তো। একেবারে attention-এ দাঁড়িয়ে পড়লাম।
কেশবদাকে ভালো লাগত। আদর্শ যাঁর উজ্জ্বল তাঁকে ভক্তি করা স্বাভাবিক। তাঁর ডাকে একবার নিঃশব্দে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি চাপা গলায় বলেছিলেন,’বন্দুক ছুঁড়তে জানিস?’
একটু অবাক হয়েছিলাম, মনে মনে ভেবেছিলাম–দু-দুটো বন্দুক আমাদের বাড়িতে, আর বন্দুক ছুঁড়তে জানি না? কিন্তু সত্যি কথা বলতে কী, আমাদের বন্দুক দুটি ছিল অহিংস, আমাদের মতোই বৈষ্ণব। তা ছাড়া কেশবদার নিকট মিথ্যে বলাটাও ঠিক হবে না। বললাম,–না কেশবদা। এখনও শিখিনি।
আয় শিখিয়ে দেব।
একটু ভয় হল, তবু কেশবদার পেছন পেছন জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে বসলাম।
এটাকে কী বলে জানিস? ছোট্ট একটা চকচকে বন্দুক বার করলেন কেশবদা। এবার রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম। শঙ্কিত নয়নে চারদিকে তাকাতেই হেসে বলেন কেশবদা, ‘ভয় নেই, তুই দেখ না ভালো করে।
কেশবদা পিস্তলটা গুঁজে দিলেন আমার হাতে।
কয়েকটা দিনমাত্র কেশবদার শিষ্যত্ব করেছি। তারপর একদিন সকালবেলা শুনি, কেশবদার বাড়ি ঘেরাও করে তাঁকে ধরে নিয়ে গেছে ইংরেজ সরকার–দেশপ্রেমের অপরাধে।
আজও সেই কেশবদাকে দেখছি। বার্ধক্য এসেছে, তাঁর দেহে নয় শুধু, মনেও। ছোটোদের কয়েকটা ইজের আর প্যান্ট নিয়ে মানিকতলার মোড়ে দাঁড়িয়ে ফেরি করছেন। নিঃসম্বল দেশকর্মী সংসারের ঘানি টানবার আর কোনো উপায়ই খুঁজে পাননি। এমনি কত ব্যর্থতার ইতিহাস জমে আছে সংসারের স্তরে স্তরে। জীবনের মাশুল দিয়ে কত জনেই তো পেল শুধু লাঞ্ছনা আর অপমান কে তার হিসাব রাখে? তবু আজ গাঁয়ের পরিচয়ে কেশবদার পরিচয় না দিয়ে পারলাম না।
শুধু কেশবদার দেশপ্রেম নয়, কত ইন্দ্রনাথের মাছ চুরির কাহিনি বাতাসে বাতাসে ঘুরে বেড়ায় আমার গাঁয়ে, কত কবির কল্পনা অনাদৃত অবস্থায় ছড়িয়ে আছে এর ঘাটে-পথে, কিন্তু বাইরের জগতের সঙ্গে কে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দেবে?
ভোরবেলা আমার ঘুম ভাঙত বৈতালিকের গীতে। রাত্রিশেষে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভৈরবীর সুর ছড়াত আমাদের হরেকৃষ্ণ বৈরাগী। তার গানের বিষয়বস্তু ছিল–রজনি প্রভাত হয়ে এল, পাখিরা শিস দিতে আরম্ভ করেছে, একটু পরেই পুবের আকাশ লাল হয়ে উঠবে, হে রাধাকান্ত! রাধিকার হৃদয়বল্লভ! আর কত ঘুমোবে, এবার তুমি জাগো। হরেকৃষ্ণ আর কার ঘুম ভাঙায় জানি না। রাধিকার হৃদয়বল্লভ তো সর্বত্রই আছেন, কিন্তু হরেকৃষ্ণের সুর আজ আর সেখানে ঝংকৃত হয় না কেন?
ষোলোখানা পুজো হত আমাদের গ্রামে। সে এক রাজসিক ব্যাপার! প্রায় শ-খানেক ঢাকের বাজনায় সমস্ত গ্রামটি সারারাত্রি সজাগ হয়ে থাকত। নবমীর রাত্রিতে শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যেত অফুরন্ত আনন্দে। কুঞ্জদা হয়তো হঠাৎ বিচিত্রভঙ্গিতে একটু ‘লোকনৃত্যম’ দেখিয়ে দিতেন তাঁর পূজ্যপাদ খুডোমশায়কে, অনন্ত হয়তো রাত এগারোটায়ই এঁদো পুকুরটায় গা ডুবিয়ে জোর গলায় সূর্যস্তব শুরু করে দিত। অবশ্য এসব তাদের ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়, পরোক্ষে কোনো একটি তীব্র রসসুধা গ্রহণের প্রত্যক্ষ ফল।
কেষ্ট ডাক্তারের ঘরের আড্ডটি ভেঙে গেছে। সেখানকার নড়বড়ে চেয়ারগুলো হয়তো এতদিনে নতুন সুরে কথা বলতে শুরু করেছে। কী জ্বালাতনটাই না করতাম ডাক্তারকে! সকলের সেরা ছিল অনাথ, ভগবান তাকে মোটেই সুস্থ থাকতে দেননি। তার ছোঁয়াচ লাগলেই চেয়ারটেবিলগুলো চিৎকার জুড়ে দিত। আলমারিগুলো পর্যন্ত তটস্থ হয়ে থাকত অকাল-মৃত্যুর আশঙ্কায়। ডাক্তার ছিল আমাদেরই বয়সি, ডাক্তারির চেয়ে আমাদের সে বেশি পছন্দ করত, আর সেজন্যেই আড্ডাটি জমত ভালো। আজ আর সেখানে আড্ডা জমে না। সেই অহেতুক উচ্ছ্বাস অসময়েই থেমে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, ডাক্তারের কাছে আমরা এখন পরদেশি।
মনে পড়ে সরলা পিসির কথা। একটি লিচু কি আম তার গাছ থেকে নিয়েছ কী আর রক্ষা নেই। চিৎকার করে পাড়া মাথায় করে তুলবে। বার বার বলবে,–‘আমার নাম সরলা। পাঁচু চ্যাটাজ্জির নাতনি আমি। আমি কাউকে ভয় করি নে। বখাটে ছেলেদের তোয়াক্কা রাখি আমি!’ কথাটা ইতিপূর্বে আরও শুনেছি, মেঘনাদবধকাব্যে প্রমীলা সুন্দরী বলেছিল,–‘রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী; আমি কি ডরাই সখি ভিখারী রাঘবে?’ সরলা পিসির কথাটা এরই আর এক সংস্করণ বলে বখাটে ছেলেরা ধরে নিত।
গ্রামটি সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল ফুটবল খেলায়। মহকুমায় সে সর্বশ্রেষ্ঠ। মহকুমায় সীমা ছাড়িয়েও তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। দূরের কোথাও কোথাও খেলতে গেলে কুলপদ্দির নাম শুনেই অগণিত লোক হত মাঠে। শুনেছি গাঁয়ের দু-একজন খেলোয়াড় ইদানীং কলকাতা এসে কোনো কোনো দলে নাম লিখিয়েছে। আমাদের ফরওয়ার্ড প্রিয়লালই যে একদিন মেওয়ালাল হয়ে দাঁড়াবে না তাই-বা কে বলতে পারে?
গাঁয়ে সর্বজনীন আনন্দের সাড়া জাগত বিজয়া-সম্মিলনী আর নববর্ষ উৎসবে। এর উদ্যোগপর্ব যা চলত তা মহাভারতের উদ্যোগপর্বকেও হার মানায়। গাঁয়ের মাঝখানে কোনো বিরাট নাটমন্দিরে দু-তিন দিন ধরে এর অনুষ্ঠান চলত। জলসা ও অভিনয় তো হতই, তা ছাড়া আবৃত্তি, রসরচনা, হাস্যকৌতুক ইত্যাদির প্রতিযোগিতায় শহরের এবং আশপাশের গাঁয়ের শিল্পীরাও এসে যোগ দিতেন।
খেজুরের গুড় ও ইলিশ মাছের জন্যে প্রসিদ্ধ এই অঞ্চল। আড়িয়ালখাঁর জলে হাজার হাজার জেলে-ডিঙি ইলিশ মাছের আশায় ঘুরে বেড়াত। লাইনের স্টিমারগুলো রাস্তা না পেয়ে ভোঁ ভোঁ করে চিৎকার করত। সে চিৎকার এখনও কানে বাজে।
আমার জীবনের স্মৃতি ওই আড়িয়ালখাঁর সঙ্গে মিশে আছে। আড়িয়ালের জলে মুছে যেত আমার দেহের ধূলি, শান্ত হত মনের আবেগ। শিশুকালে এর তীরে বসে কত খেলা করেছি, চলতি স্টিমারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কত দৌড়েছি, কৈশোরে তার রুদ্রমূর্তি দেখে ভীতও হয়েছি; কতদিন এর তীরে বসে দিগন্তের মন-মাতানো ছবি দেখেছি। আজ কোথায় গেল সেসব, কত দূরে সেই আড়িয়ালকে ফেলে এসেছি। গাঁয়ের ওই ঘন জঙ্গলের মধ্যে যে এত শান্তি আছে, ওই নিরক্ষর গ্রামবাসীর অন্তরে যে এত ভালোবাসা আছে, ওই আড়িয়ালখাঁর ঘোলাটে জলে যে এত আকর্ষণী শক্তি আছে, তা এতদিন এমন করে অনুভব করিনি, আজ দেখি, আমার সমস্ত মন জুড়ে আছে সেইসবেরই স্মৃতি!
আমার সেই সাধের গ্রাম ধ্বংসের মুখে। আমার বাল্যের লীলাভূমি, কৈশোরের খেলাঘর, যৌবনের স্বর্গ পরিত্যক্ত, শূন্য-লোকালয়। এক নিষ্ঠুর আঘাতে সে আজ মৃতপ্রায়। শুধু আমার গ্রামের নয়, এমনি কত শত শত গ্রামের লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর বুকে আজ জ্বলছে অনির্বাণ চিতা, কণ্ঠে শুধু হা-হুঁতাশ, চোখে জল! কিন্তু সবই কি ভাগ্য? যদি তাই হয় তবে এই নিষ্ঠুর আঘাত আমি মেনে নিতে পারব না। দেশের ভাগ্যনিয়ন্তাদের ওপর থাকবে আমার চিরন্তন অভিশাপ, ভাগ্যের বিরুদ্ধে থাকবে বিদ্রোহ! আর আমার হতভাগ্য দেশবাসীকে অনুরোধ করব স্মরণ করতে কবিগুরুর সেই বাণী–’ভাগ্যের পায়ে দুর্বল প্রাণে, ভিক্ষা না যেন যাচি।
বগুড়া – ভবানীপুর
কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এদেশকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন–স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে গড়া এবং একথাও বলেছেন, এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। বাংলাদেশের এক স্বপ্নাচ্ছন্ন গ্রাম হল এই সতীতীর্থ ভবানীপুর। গ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে শুনেছি যে দক্ষের পতিনিন্দায় লজ্জায় ও ক্ষোভে আত্মবিসর্জন দিলেন সতীদেবী। মহাপ্রলয় হল শুরু। সতীর নশ্বর দেহ নিয়ে নৃত্য করে স্বর্গ-মর্ত্য পৃথিবী জুড়ে তান্ডব সৃষ্টি করলেন সংহারক মহাদেব। রক্ষাকর্তা বিষ্ণুর টনক নড়ল। চক্রের আবর্তনে খন্ডিত হল সতীদেহ আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পেল ধরিত্রী। একান্ন খন্ডের একখন্ড পতিত হল উত্তরবঙ্গের অখ্যাত এই ভবানীপুর গ্রামে। মা ভবানী স্কুলদেহ পরিত্যাগ করে দারুদেহের রূপ পরিগ্রহ করলেন। আমার গ্রামের ঐতিহাসিক পটভূমিকা তৈরি হল। আমার জন্মভূমি ভবানীপুর তাই পীঠস্থান। সেখানকার মাটি, সেখানকার ইতিহাস সবই আছে, কিন্তু নেই শুধু আমার বাসের অধিকার। আমার শান্তির নীড় আজ নষ্ট। খুব বেশিদিনের কথা নয়, বছর কয়েক আগেও ভাবতে পারিনি যে এমন সোনার গাঁ ছেড়ে আমাকে হীনতা দীনতার মধ্যে জীবনের শেষদিনগুলো কাটাতে হবে। আমার জন্মভূমি থাকতেও আমি পরবাসী লক্ষ্মীছাড়া হয়ে ক্লান্তপায়ে ফুটপাথে বিশ্রাম করব, বৃক্ষতলে রাত কাটাব, শিশুপুত্রের হাত ধরে ঘুরে বেড়াব অস্নাত অভুক্ত অবস্থায়। এই অশ্রুর বন্যায় মনে পড়ছে একটি কবিতার কথা,
ত্রিযুগের ব্যথা তিনভাগ জলে পূর্ণ করিল ধরা,
বাকি একভাগ ধর্মের নামে আজ অশ্রুতে ভরা।
আজ দেখছি অশ্রুই সত্যি। না হলে এমন যে স্বপ্নঘেরা গ্রাম ভবানীপুর, এমন শাঁখারীপুকুর তাকে ছেড়ে নতুন ইহুদি সেজে আমাদের অচেনা-অজানা পরিবেশে চলে আসতে হবে কেন? শান-বাঁধানো কলকাতার কোলাহলমুখর অশান্ত সন্ধ্যায় যখন মন বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তখনই বেশি করে মনে পড়ে সেই শ্যামল বনানী পরিবেষ্টিত আমার জন্মভূমি আর সাধের শাঁখারীপুকুরের কথা। মন মন্থন করে চলে শৈশবের সুখের দিনগুলো। মনে হয় কাক জ্যোৎস্না রাত্রে চুপচাপ বসে আছি শাঁখারীপুকুরের ধারে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে অবচেতন মনের সেই পরিচিত ছবি, ‘আমি শাঁখের শাঁখারী-রাঙা শাঁখা ফিরি করি।’ সঙ্গে সঙ্গে বনমর্মর ভেদ করে কানে যেন ভেসে আসে ক্ষীণ স্বর–এই দেখো আমার শাঁখা পরা হাত!’ সংবিৎ ফিরে চমকে উঠে দেখি বাস্তবতার কঠোর পরিবেশ যেন ঠাট্টা করছে আমাকে। চোখ দুটো জলে ভরে আসে আপনা-আপনি। মনে মনে শুধু আক্ষেপের সুরে বলি,
অনাদি এ ক্রন্দনে মিশাইনু ক্রন্দন এ,
বুঝে নে মা এ প্রাণের কী দাহ!
মাঝে মাঝে ভাবি আমার গ্রামের ইতিহাস আমার ওপর এমন মর্মান্তিক প্রতিশোধ কেন নিল? আজ শত দুঃখের মধ্যেও সেরপুরের সেই ফ্যামা পাগলা আমওয়ালার কথা বড়ো বেশি করে মনে পড়ছে। কোথা থেকে খুঁজে খুঁজে সিঁদুরকুটি আম নিয়ে এসে অতি আপনজনের মতোই সে যেন বলছে ‘খোকাবাবু, কনে যাও, আম খ্যাবা না?’ কই সে তো কোনোদিন বলেনি, বাবু, ‘আমাদের মোছলমানের দ্যাশ–তোমরা হেঁদুস্থানে চল্যা যাও!’
সেই কাদের মিয়া, রাজেক মাস্টার তারা তো কেউ আমার মন থেকে মুছে যায়নি। তাদের প্রতিটি কথা প্রতিটি উপদেশ আজও আমি মনে করে রেখেছি। আজও তাদের কথা চিন্তা করে আমার স্পর্শকাতর মন বেদনায় টনটন করে ওঠে। কেন?
কেন আমার প্রিয় সহপাঠী মহসিনের শেষ কথাগুলো আজও বার বার মনে পড়ছে এত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও? আমাদের চলে আসার সময় সে বলেছিল– হ্যাঁরে, আমরা কী দোষ করেছি যে তোরা চলে যাচ্ছিস? এর উত্তর এ অবধি খুঁজে পাইনি আমি। ভাই মহসিন, যেখানেই থাকো তুমি, জেনো এখনও তোমাকে আমি ভুলিনি। তোমার সঙ্গে আমাকে শত্রুরা পৃথক করতে পারেনি। ভাই ভাইকে কবে কোথায় কে ভুলতে পেরেছে? তুমি যদি কোনোদিন আমাকে স্মরণ করো তাহলে নিশ্চয়ই আমি যাব। কী আর বলব, কী সমবেদনা জানাব, শুধু ভাবছি আমিও বাঙালি। বাঙালি ঘর ছাড়তেও পারে, আবার তৈরি করতেও জানে।
চোখ বুজলেই মনে পড়ে নাটমন্দিরের ধারে রক্তচন্দনের বীজ কুড়োনোর সে কী ধুম। কে কত বেশি কুড়োতে পারে তার যে প্রতিযোগিতা চলত তা ভাবতে গেলে হাসি পায় আজ। হারান পন্ডিতমশায়ের বাড়ি থেকে পেয়ারা চুরি করতে গিয়ে কতদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা একপায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। এসব শাস্তি কিন্তু কোনোদিনই পেয়ারা চুরি থেকে আমাদের দূরে সরাতে পারেনি। পেয়ারা গাছটি কি তেমনিভাবে ফল দিয়ে চলেছে? ছোটো ছেলের দল আজও কি সেই সেখানে গিয়ে ভিড় জমায় পেয়ারা সংগ্রহের জন্যে?
পাঁজিতে প্রতিবছরই পুজো আসে, কিন্তু আমরা দেশে যেতে পারি না। আজ দেশ স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু আমরা কি স্বাধীন, আমরা যে সম্পূর্ণ অন্যের করুণার ওপর নির্ভরশীল। আগে প্রতিপুজোতেই বাড়ি গিয়েছি। সে কী আনন্দের দিন! ছোটো থেকেই দেখে আসছি অন্য সব দিনেও মা করতেন শিবপুজো। আমরা বসে থাকতাম ঠাকুরের প্রসাদ আর রক্তচন্দনের লোভে।
কালীবাড়ি আর কাছারির মালিক ছিলেন নাটোরের ছোটোতরফ। তাদের কথা ভোলবার নয়। আর ভুলতে পারব না রামনবমীর উৎসবে ব্যস্তসমস্ত নায়েব চোংদারমশায়কে। তাঁর কছে হিন্দু-মুসলমান সবাই ছিল সমান। জাতির লেবেল এঁটে তাঁর কাছে কেউ বিশেষ আদর আশা করতে পারত না। রামনবমীর দিন সমস্ত জায়গাটি গম গম করত। আজও মাঝে মাঝে চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেদিনকার ছবি জীবন্ত হয়ে।
দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে পড়ে সেদিনকার কথাকেও আজ রূপকথা বলে মনে হচ্ছে। আমাদের। সকালে স্নান-আহ্নিক সেরে মা সবাইকে নিয়ে বসে কুটনো কুটতেন। ঝিয়েরা রাশি রাশি বাসন ধুয়ে রকের ওপর রাখছে। সেসব বাসন আর একবার ভালো করে ধোয়া হলে তবে হেঁসেলে যাবে। বাইরে থেকে চাকর-ঠাকুররা এসে রান্না ও অন্যান্য কাজে সাহায্য করত। প্রকান্ড উঠোন–ভেতরের বাড়িতে ধানের মরাই বাঁধা সারি সারি। একপাশে চেঁকিশাল, গোয়ালে গোরু, পুকুরে মাছ। ঠাকুমা প্রতিটি গোরুর গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করে তবে অন্য কাজে মন দিতেন। যেখানে পশুর প্রতিও মানুষের এমন অসীম মমতা, মানুষে মানুষে প্রীতি-প্রেমের এমন শোচনীয় অভাব সেখানে ঘটে কী করে! বাইরের বাড়িতে মাঝে মাঝে কীর্তনের দল এসে মাতিয়ে তুলত মন! তার সব খুঁটিনাটি ছবি বড়ো বেশি করে আজকে পীড়িত করে তুলছে সারাঅন্তরকে। মনে করি আর ভাবব না ওসব কথা, কিন্তু মনের ওপর চোখ রাঙিয়ে বেশিক্ষণ থাকতে পারি না তো! মানুষের মন কি পালটায়?
চিরদিনই ইতিহাস রচনা করেছে মানুষ। আজকের ‘ছেড়ে আসা গ্রাম’কে নিয়ে জানি একদিন ঐতিহাসিকের দল গবেষণা করবেন, সাহিত্য পাবে খোরাক। কিন্তু তখন কি আর আমরা থাকব? যে সংঘবদ্ধ জীবন জাতিধর্ম নির্বিশেষে একসূত্রে সহস্রটি মনকে বেঁধেছিল সে সূত্র কে ছিঁড়ল? এক এক সময় হিসেবি মন কী পেয়েছি আর কী পাইনি তার হিসেব করতে যায়, কিন্তু তার সার্থকতা কোথায়? ছিন্নমূল জীবনে স্থিতি না এলে হিসেব তো মিলবে না। মন শুধু ক্ষুব্ধ হয়েই বলবে,
প্রলয় মন্থন ক্ষোভে
ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি
পঞ্চশয্যা হতে। লজ্জা শরম ত্যাগি
জাতি-প্রেম নাম ধরি প্রচন্ড অন্যায়
ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।
বরিশাল জেলা – বাণারিপাড়া গাভা কাঁচাবালিয়া মাহিলাড়া চাঁদসী সৈওর নলচিড়া
পরপারের ডাক এলে মানুষকে সব কিছু ছেড়ে এ সংসার থেকে বিদায় নিয়ে চলে যেতে হয় মহাপ্রস্থানের পথে তা জানি, আর জীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝি তার জন্যে শোক করে কোনো লাভ নেই, হয়তো তা বৃথা; কেননা আলোর অপরদিকে যেমন আঁধার, জীবনের অপরদিকে তেমনি মরণ–যে চলে যায় তাঁর স্মৃতি শুধু পড়ে থাকে, তাঁর সন্ধান মেলে না আর কোনোকালে।
শতাব্দীব্যাপী সাধনায় যে স্বাধীনতা পেয়েছি আমরা, সে স্বাধীনতার যজ্ঞাহুতিতে আত্মবিসর্জন দিয়েছে বহু বীর, ত্যাগ ও দুঃখ ভোগ করেছে বহু দেশকর্মী, লাঞ্ছনা ও নির্যাতন হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছে অগণিত নর-নারী। এ চরম ও পরমবস্তু লাভের জন্যে পার্থিব ক্ষয়ক্ষতিকে মাথা পেতে নিতে কুণ্ঠা বোধ করেনি ভারতবাসী, বিশেষ করে বাঙালি। ত্যাগের মহিমায় প্রদীপ্ত করেছে তারা দেশকে, জননী ও জন্মভূমি তাদের চোখে এক ও অভিন্ন, জন্মদায়িনী ও দেশমাতৃকা ‘স্বর্গাদপি গরীয়সী’ তাদের কাছে।
পরাধীনতার বন্ধনমুক্তির জন্যে ধূপের দহনের মতো নিপীড়ন সহ্য করেছে যেমন অগণিত দেশবাসী তেমনি দুঃসহ ব্যথার মধ্যে দেশমাতৃকার স্বাধীনতাকে বরণ করে নিয়েছি আমি। স্মরণীয় সেই ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা উৎসবের দিনে আনন্দে মুখরিত কলকাতা মহানগরীর রাজপথ দিয়ে মাতৃহারার ব্যথা, বুকে নিয়ে চলেছিলাম শ্মশানযাত্রায়। শ্মশানে শায়িতা সেই করুণাময়ী স্নেহময়ী মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে শেষবারের মতো ভেবেছিলাম, এক মাকে হারিয়েছি আর এক মা হয়তো আমার আছে, যে মায়ের সান্নিধ্যে গিয়ে স্নেহের নীড়ে মাথা এঁজে ভুলতে পারব মনের যত ব্যথা। কিন্তু কোথায় সে সান্ত্বনা? গর্ভধারিণী মাকে হারাবার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভূমি, পিতৃপুরুষের জন্মভূমিকেও হারিয়েছি। দেশমাতৃকা দ্বিখন্ডিত হয়ে আমাদের জন্মভূমি চলে গেছে আজ অন্য রাজ্যে, পরশাসনে। শ্মশানচুল্লির ধূমায়িত পিঙ্গলাগ্নি আমার যে মায়ের দেহকে ছাই করে দিয়েছে, জানি আমি জানি, এ জীবনে তাঁর আর সন্ধান পাব না; কিন্তু রাজনীতির পাকচক্রে শ্মশানের চেয়েও ভয়াবহ আগুনের লেলিহান শিখায় হাজার হাজার নর-নারী ও শিশুর জীবন পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে, আমাদের ঘরছাড়া, দিশেহারা হতে হবে তা ভাবতে পারিনি কোনোদিন। ঝড়ের মধ্যে নীড়হারা রাতের পাখি যেমন করে বিলাপ করে ফেরে বন থেকে বনান্তরে, আমরাও তেমনি দেশবিভাগের অভিশাপে অজানার স্রোতে ভেসে চলেছি দেশ থেকে দেশান্তরে, স্থান থেকে স্থানান্তরে; আর দৈনন্দিন জীবনে বহন করে চলেছি ছিন্নমূল উদবাস্তু জীবনের শত বিড়ম্বনা ও লাঞ্ছনা। জানি না কবে হবে এই মহানিশার অবসান!
শান্ত, স্নিগ্ধ, ছায়াসুনিবিড় আমার পল্লিগ্রাম ও সরল অনাড়ম্বর একান্ত পরিজনদের ছেড়ে এসে কোলাহলমুখর মহানগরীর লক্ষ লোকের ভিড়ের মধ্যে আজ হারিয়ে ফেলেছি নিজেকে –গতানুগতিক কর্মক্লান্ত একটানা জীবন নিয়ে কোনোমতে কষ্টে-ক্লিষ্টে বেঁচে আছি। বিস্মৃতপ্রায় কবে কোন ছেলেবয়সে কবিতায় পড়েছিলাম, ‘ভবিষ্যতের লক্ষ আশা মোদের মাঝে সন্তরে, ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সে রঙিন স্বপ্ন আজ চলে গেছে, বাস্তবের অভিজ্ঞতায় আজ বুঝতে পারছি কল্পনা ও বাস্তব এক নয়, আমাদের যাত্রাপথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, কণ্টকাকীর্ণ–জীবনযুদ্ধের প্রতিপদক্ষেপে রয়েছে কঠিন দ্বন্দ্ব, প্রবল প্রতিযোগিতা।
কর্মক্লান্ত জীবনের ক্ষণিক অবকাশে মাঝে মাঝে যখন আনমনে মহানগরীর ফুটপাথ দিয়ে চলি কিংবা গঙ্গার ধারে গিয়ে বসি তখন আমার মা আর আমার পল্লিগ্রাম বানারিপাড়ার স্মৃতি আমার মনে জাগে। এই স্মৃতি আমার সমস্ত অস্তিত্বকে যেন আচ্ছন্ন করে দেয়। কত কথাই না মনে পড়ে তখন, আর ভাবতে ভাবতে চোখ জলে ভরে আসে।
বাল্য ও কৈশোরের সামান্য কয়েকটা দিন কাটিয়েছিলাম আমার পল্লিগ্রাম বানারিপাড়ায়। বাবা থাকতেন বিদেশে, তাই বাকি সময়টা তাঁর সঙ্গে ঘুরেছি নানা জায়গায়, পড়াশুনাও করেছি নানা শিক্ষায়তনে। কিন্তু বাল্যকালের সেই পল্লিজীবনের স্মৃতি আজও অম্লান হয়ে জাগ্রত আছে আমার মানসপটে। পাগলামি স্বভাবের নিশ্চিন্ত দিনগুলোতে যে গ্রামের ধুলোমাটি গায়ে মেখে বাল্যবন্ধুদের সঙ্গে একত্রে খেলা করেছি, পুকুরে স্নান করেছি, স্কুলে গেছি, সেই সাতপুরুষের ভিটের মায়া আজও যে ভুলতে পারিনি। পিতৃপিতামহের আশিসপূত তাঁদের যুগযুগান্তরের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত বাণারিপাড়ার সঙ্গে আমার অন্তরের ও নাড়ীর যোগ, এ গ্রাম আমার বাল্যের মনভোলানো মায়াপুরী, এ গ্রাম যে আমার কাছে তীর্থভূমি–এর প্রতিটি ধূলিকণা আমার কাছে পবিত্র, তাই কী করে ভুলব, কী করে ভুলতে পারব আমার ছেড়ে-আসা বানারিপাড়া গ্রামকে? সন্তান যেমন ভালোবাসে মাকে, আমি তেমনি ভালোবেসেছি বাণারিপাড়াকে।
লক্ষ গ্রামের বাংলাদেশে আমার গ্রাম বানারিপাড়া একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যে শুধু বরিশাল জেলায় নয়, সমগ্র বাংলার মধ্যে বাণারিপাড়া অনন্য।
বরিশাল জেলায় যে যায়নি সে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ‘সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং শস্য শ্যামলাং মাতরম’ বাংলা মায়ের এই রূপ বর্ণনা প্রত্যক্ষ করেনি। প্রকৃতি দেবীর অকুণ্ঠদানে প্রতিদিন দু-দুবার করে জোয়ার-ভাটার খেলায় বরিশালের গ্রামপ্রান্তর সুজলাং, বরিশালের মলয় শীতলাং ও বরিশালের মাটি সুফলাং শস্য-শ্যামলাং হয়েছে। রসপুষ্ট বরিশালবাসী তাই দূর-দূরান্তরে থেকেও বরিশালের মাটিকে ভুলতে পারে না। সেই বরিশালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপদ বাণারিপাড়া।
আমার গ্রামের পশ্চিমে বিস্তৃত খরস্রোতা নদী-দূর-দূরান্তরে যাবার স্টিমার পথ, আর গ্রামের মধ্য দিয়ে উত্তর ও পূর্বদিক ঘেঁষে ছোটো স্রোতস্বিনী খাল চলে গেছে–বরিশাল শহরে যাবার নৌকাপথ এটা। এই খাল ও নদীর সংযোগস্থলে খালের দু-পাশে বিরাট বন্দর। এর বিপরীত দিকে গ্রামের পূর্ব সীমানায় সপ্তাহে দু-দিন হাট বসে এবং এই হাটে হাজার হাজার মন ধান চাল কেনাবেচা হয়ে থাকে। বন্দর ও হাটকে যুক্ত করে গ্রামের মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা হয়ে গেছে সিমেন্ট বাঁধানো একটি রাস্তা। এই পথ ক্রমে দীর্ঘ হয়ে বরিশাল শহরে গিয়ে মিশেছে। বর্ষা-অন্তে মোটরযোগে বরিশাল শহরে যাতায়াতে এই পথই প্রশস্ত। গ্রামের কিছু দূরে উত্তরে চাখার, খলিসাঁকোটা, উজিরপুর; পূর্বে নরোত্তমপুর, গাভা, কাঁচাবালিয়া, দক্ষিণে আলতা, আটঘর, স্বরূপকাঠি ও পশ্চিমে বাইসারি, দস্তোঘাট, ইলুহার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রামগুলো বানারিপাড়াকে মধ্যমণি করে স্ব স্ব ঐতিহ্যের বাহকরূপে দীপ্যমান রয়েছে। গ্রামের দক্ষিণাংশে বাস বিখ্যাত নট্টসম্প্রদায়ের, যাদের সুমধুর ঢোল বাজনা ও যাত্রাগান বাংলাদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। গ্রামের চারদিকে রয়েছে বিভিন্ন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, তারা বংশপরম্পরায় হাট-বন্দরের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করে গ্রামকে সর্বদা প্রাণচঞ্চল রেখেছে। আর সেই সুন্দর পাকা রাস্তার দু-ধারে ও গ্রামের অন্যত্র ছড়িয়ে আছে বাংলার সুপরিচিত বুদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, যারা সংস্কৃতি ও শিক্ষায় সমাজে খ্যাতিলাভ করেছে। এদের মধ্যে গুহঠাকুরতা বংশই সংখ্যায় গরিষ্ঠ, প্রতিষ্ঠায় শ্রেষ্ঠ ও সর্বত্র সুপরিচিত।
এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টায় গ্রামে নানাবিধ শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এদেরই অনুপ্রেরণা ও স্বার্থত্যাগে প্রায় সত্তর বৎসর পূর্বে এ গ্রামে স্থাপিত হয়েছে প্রথম উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়। দুটি বৃহৎ দালানে অবস্থিত রয়েছে এই বিদ্যালয়টি। গ্রামান্তরের বহু ছাত্রকে দেখেছি বাণারিপাড়ার ঘরে ঘরে থেকে শিক্ষালাভ করেছেন। স্বর্গীয় বসন্তকুমার গুহঠাকুরতা ও রজনীকান্ত গুহঠাকুরতা প্রভৃতি বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিবৃন্দের সাহায্যে একদিকে ক্রমশ শ্রীবৃদ্ধি হয়েছ এ বিদ্যালয়টির, অপরদিকে পরবর্তীকালে জাতীয় বিদ্যালয়, হরিজন বিদ্যালয়, মনোরঞ্জন শিল্পসদন, একটি অবৈতনিক বালিকা বিদ্যালয় ও শ্রীভবন নামে একটি উচ্চ ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। বাণারিপাড়ার পাবলিক লাইব্রেরিটিও স্থাপিত হয়েছে প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে। পরে আরও একটি লাইব্রেরি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিনামূল্যে দরিদ্র জনসাধারণের চিকিৎসার জন্যে জেলাবোর্ডের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি দাঁতব্য চিকিৎসালয়, যাতায়াতের সুবিধার জন্যে খালের ওপর নির্মিত হয়েছে চার চারটে প্রকান্ড লোহার পুল। পূর্বে বাজারের কাছে যে রমণীয় দোলায়মান লোহার পুলটি ছিল তা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংগঠনমূলক কাজ এগিয়ে চলেছে একদিকে, অন্য দিকে গ্রামে আনন্দ বিতরণের জন্যে লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট অবদান কীর্তনগান, কবিগান, যাত্রা ও থিয়েটার প্রভৃতির ব্যাপক প্রচলনও হয়েছে।
১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশি আন্দোলন থেকে শুরু করে অসহযোগ ও আইন অমান্যের কাল পর্যন্ত যাবতীয় রাজনৈতিক আলোড়নে বানারিপাড়া বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে এসেছে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে এ গ্রামের অবদান সত্যিই বিরাট। ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দে দার্জিলিং-এ লেবং নামক স্থানে তদানীন্তন গভর্নর অ্যাণ্ডারসনকে হত্যা করতে গিয়ে ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য নামে ১৬ বৎসর বয়সের যে যুবক ফাঁসির মঞ্চে জীবন বিসর্জন দেয় সে-যে এই গাঁয়েরই আত্মভোলা ছেলে! আইন অমান্য, বিলিতি দ্রব্য বর্জন মাদকদ্রব্যের দোকানের সামনে পিকেটিং, ঘরে ঘরে লবণ তৈরি, সুতোকাটা প্রভৃতি বিষয়ে কেশব ব্যানার্জি, কালাচাঁদ ভট্টাচার্য, ক্ষিতীশ ঠাকুরতা, কুমুদ ঠাকুরতা, ইন্দুমতী গুহঠাকুরতা, নলিনী দাশগুপ্ত ও অন্যান্যকর্মীবৃন্দ যে অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
সে-যুগে সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা–বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বরিশাল সম্মেলনের সময় সরকারি আদেশ অগ্রাহ্য করে বন্দেমাতরম’ ধ্বনি উচ্চারণের জন্যে পুলিশের লাঠিতে নিগৃহীত চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা তাঁরই অমরকীর্তি সন্তান। পুলিশের প্রহারে জর্জরিত-দেহ, তবু বন্দেমাতরম’ ধ্বনির বিরাম নেই। সুতীব্র প্রতিবাদে জানিয়ে দিলেন তিনি,
বেত মেরে কি মা ভুলাবে,
আমরা কি মা’র সেই ছেলে?
তাঁরই গ্রামবাসী আমরা কী করে ভুলে থাকব আমাদের গ্রাম-মাকে?
সুভাষচন্দ্র বসুর পদার্পণে ধন্য হয়েছে আমার গ্রাম। খুব ছোট্ট ছিলাম তখন, কিন্তু আজও বেশ স্পষ্ট মনে আছে–জাতীয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বক্তৃতা দেওয়ার পর আমাদের পাশের বাড়ির দালানের বারান্দায় জ্যোৎস্না রাত্রে ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে বিশ্রাম করছিলেন সুভাষচন্দ্র, তাঁর আশপাশে ছিলেন আরও কয়েকজন। জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত আকাশের দিকে তাকিয়ে সুভাষচন্দ্র ক্ষীণকণ্ঠে গেয়ে উঠলেন—’এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভালো।‘ পাশে দাঁড়িয়ে আমার এক দাদা প্রশ্ন করলেন–কী মরণ? সুভাষচন্দ্র উত্তর দিলেন, ‘যে মরণ স্বরগ সমান।’ সুভাষচন্দ্র আজ জীবিত কি লোকান্তরিত জানি না, কিন্তু দেশমাতৃকার বন্ধনমুক্তির জন্যে মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে রাত্রির আলো-আঁধারেই তিনি দেশ থেকে বহির্গত হয়েছিলেন। আজ দেশবাসীর কাছে নেতাজিরূপে বন্দিত তিনি, কিন্তু তাঁকে দেশগৌরব মুকুটমণি প্রথম পরিয়েছিলেন কলকাতা মহানগরীর এক জনসভায় আমাদেরই গ্রাম-গৌরব স্বৰ্গত চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা।
অপূর্ব শোভামন্ডিত আমার ছেড়ে-আসা গ্রামে আবির্ভাব হয়েছে বহু স্মরণীয় ও বরণীয়ের –জীবনের এক-একটি ক্ষেত্রে তাঁদের এক-একজনকে পথিকৃৎ বললেও বোধ করি অত্যুক্তি হবে না।
থানা, ডাকঘর, হাটবাজার, স্কুল ইত্যাদি নিয়ে আমার গ্রামটি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। পল্লিসৌন্দর্যের এক অফুরন্ত ভান্ডার–সুখশান্তিতে নিরুপদ্রবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছে গ্রামবাসীরা। গ্রামের আশপাশে রয়েছে বিভিন্ন আশ্রম। গ্রামের মধ্যে আছে স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন চকমিলানো বানিয়াবাড়ি। এ বাড়ি গ্রামের একটি গৌরবের বস্তু। দূর-দূরান্তরের গ্রামের লোকেরা নৌকাপথে এর সমুখ দিয়ে যাওয়ার সময় নৌকা থামিয়ে একবার অন্তত এ বাড়ির সৌন্দর্য না দেখে যেতে পারে না। যাত্রা-থিয়েটারের দ্রব্যসামগ্রী থেকে শুরু করে একটা সংসারের পক্ষে আবশ্যক যাবতীয় জিনিসপত্র পাওয়া যায় এখানে। জেবিডি কালির আবিষ্কারক স্বনামখ্যাত জগবন্ধু দত্ত এ বাড়ির প্রতিষ্ঠাতা।
দুর্গা পুজোর দু-দিন আগে থেকে লক্ষ্মী পুজোর পরদিন পর্যন্ত প্রবাসী ও অপ্রবাসী গ্রামবাসীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্যে জাহাজের মতো বিরাট একখানি করে স্টিমার খুলনা থেকে সরাসরি বানারিপাড়া পর্যন্ত চলাচল করত। বহুদূরের গ্রামবাসীরাও বাণারিপাড়া স্টেশনে নেমে নৌকো করে চলে যেত নিজ নিজ গ্রামে। পুজোর পরে শুরু হত নানারকমের সভাসমিতি, প্রীতিসম্মিলনী, বড়ো ও ছোটোদের নাট্যাভিনয় ও যাত্রাগান। এসব অনুষ্ঠানে মুসলমানেরাও যোগ দিয়েছে প্রতিবেশী ভাই হিসেবে, পুজোর প্রসাদ নিয়েছে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধায়। প্রসাদের প্রধান উপকরণ ছিল নারকেলের তৈরি বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী। গ্রামের মেয়েদের হাতের তৈরি নারকেলের জিনিস খেয়ে সুভাষচন্দ্র পরমতৃপ্তি পেয়েছিলেন।
ছোটো-বড়ো প্রতিটি লোকের সঙ্গেই প্রত্যেকের কী মধুর সম্পর্কই না লক্ষ করেছি গ্রামে, কলকাতার জীবনে আজ তা বিশেষভাবেই অনুভব করছি। ধোপা, নাপিত, ভূমালি এরা সবাই ছিল আপনার জন। ছোটোবেলায় এক সম্পর্কীয়া পিসির বিয়ের ছবি ভেসে উঠছে চোখের সামনে। বিয়ের আসরে আমাদের গাঁয়ের নাপিত এসে বিড়বিড় করে কী যে গৌরবচন বলে গেল তখন তা ঠিক বুঝতে না পারলেও পরে তার কাছ থেকে টুকে নিয়ে সবটা মুখস্থই করে ফেলেছিলাম। এখনও সে গৌরবচনের কিছুটা মনে পড়ে, ছড়া কেটে সে বলেছিল,
চন্দ্রসূর্য দেবগণ চিন্তাযুক্ত হৈল মন।
না হইলে নাপিতের কর্ম, শুদ্ধ হয় না কোনো বর্ণ।
ডাইনে শংকর বামে গৌরী,অদ্য মিলন হইল শিব-গৌরী।
আপনেরা চাঁদবদনে বলেন হরি হরি,
নাপিতের দক্ষিণা স্বর্ণ একভরি।
নাপিতস্য গড়গড়ি!
এই ‘নাপিতস্য গড়গড়ি’ কথাটি ছিল আমাদের হাসির খোরাক। কিন্তু সে যাই হোক, বর কনের মিলনকে শুদ্ধ করে দিয়ে নবদম্পতির জন্যে তার শুভ কামনার বিনিময়ে সে যে দক্ষিণস্বরূপ একভরি মাত্র স্বর্ণ প্রার্থনা করত তা কী আর এমন বেশি! বিবাহাদি ব্যাপারে এমনি নিজ নিজ কাজ করে থোপা, ভূমালি প্রভৃতি সব বৃত্তিজীবীই বিদায় পেত। তারা সব আজ কোথায়? তাদের কী করে চলে?
বাণারিপাড়া সম্মিলনীর কথা উল্লেখ না করলে এই গ্রামের বর্ণনা অসমাপ্ত থেকে যাবে। বাণারিপাড়ার বহু অধিবাসী ভাগ্যান্বেষণে আজ দেশের বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে পড়েছেন। বাণারিপাড়ার কয়েকজন উৎসাহী কর্মী প্রবাসে থেকেও পারস্পরিক মিলনক্ষেত্র হিসেবে এবং সেবার আদর্শ নিয়ে সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা করলেন। সেই থেকে সম্মিলনী নানাভাবে গ্রামের সেবা করে আসছে। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে আমাদের হাস্যমধুর প্রাণচঞ্চল গ্রামখানি আজ নিস্তব্ধ শ্মশান–এই শ্মশানে আবার শিবের আবির্ভাব কবে হবে কে জানে?
মনে পড়ে কতদিন ভোরে রায়ের হাটের পুলের ওপর দাঁড়িয়ে মুসলমানদের দূর হতে ভেসে-আসা নামাজের সকরুণ সুর শুনেছি–সে-সুরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সৌহার্দ্য ও মিলনের আহ্বান ছিল। দিবাবসানে কত সন্ধ্যায় সর্ব উত্তরের বাড়ির পুলের ওপর দাঁড়িয়ে ঘরে ঘরে সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টা বাজনা শুনেছি, সেই আরতির তালের সঙ্গে যেন নৃত্য করেছে আমার সারাপ্রাণ। কত রাত্রে নদীর পারে বেড়াতে বেড়াতে চোখে পড়েছে, নদীর জলে ছুটে চলেছে। শত শত চাঁদের রুপালি বন্যা। শরৎকালে কত প্রভাতে, শীতের কত মধ্যাহ্নে নদীর তীরে দাঁড়িয়ে দেখেছি প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য-সারি সারি পাল তুলে চলেছে কত অজানা মাঝির নৌকা, দূরদিগন্তের শ্যামলিমা মুগ্ধ করেছে মনকে। কিন্তু সেসবই আজ স্মৃতি। তাই তো বলতে ইচ্ছে হয়—’নয়ন সম্মুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।’ রাজনৈতিক ঘটনা বিবর্তনে সে-গ্রাম আজ আমার কাছ থেকে দূরে-বহুদূরে, কিন্তু জীবনের শত পটপরিবর্তনেও মনের পটে আঁকা থাকবে একখানা ছবি–সে-ছবিখানি আমার ছেড়েআসা গ্রাম বানারিপাড়ার।
.
গাভা
সুখস্মৃতিকে রসিয়ে রসিয়ে রোমন্থন করা বোধহয় মনের একটা বিলাস। না হলে আজ এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও, ছন্নছাড়া অব্যবস্থিত জীবনের দুর্দিনেও কেন আমার জন্মভূমি গাভার কথা এত বেশি করে মনে পড়ছে? আমার মাটির মায়ের কাছ থেকে যে শান্তি যে সান্ত্বনা যে সুখ যে বৈভব পেয়েছিলাম একদিন, তার সঙ্গে আজকের দিনের জীবনকে তুলনা করতে কেন আমি ব্যস্ত? মন আমার অতীত-মুখর,–এই নগরজীবনের সমস্ত কিছুকে অগ্রাহ্য করে বল্গাহীন ঘোড়ার উল্কার গতি নিয়ে ছুটে চলেছে মন। তার সামনে কোনো বাধা কোনো বিপত্তিই যেন টিকবে না, মানুষের গড়া ভেদাভেদের কোনো তোয়াক্কাই করে না সে। উদ্দাম ঊর্ধ্বশ্বাসে সে পরিক্রমা করছে গাভা গ্রামটিকে কেন্দ্র করে। মনে পড়ছে, শীতের এক অপরাহ্নে কলকাতার শ্মশানের বহ্নিশিখায় এক মাকে হারিয়েছিলাম। বহুদিন পরে আর এক খন্ডপ্রলয়ে পূর্ববাংলার দিগন্তবিস্তৃত হিংসার আগুনে হারালাম আমার দেশমাতাকে। জননীর সঙ্গে সঙ্গে জন্মভূমিও গেলেন আমাদের অকূলপাথারে ভাসিয়ে। অসহায় বোধ করছি নিজেদের ভাগ্যের কথা চিন্তা করে। যাঁর স্নেহাঞ্চলে বড়ো হয়েছি তাঁর প্রতি অপরিসীম আকর্ষণ থাকা বিচিত্র নয়। প্রকৃতির পরিহাস এমন নির্মমভাবে কেন আমাদের ওপর বর্ষিত হল? সংসারের অমোঘ বিধানে একদিন এই ধরাতল থেকে সকলকেই যেতে হবে–তাই জ্বলন্ত চিতাগ্নির মধ্যে গর্ভধারিণী মাকে চিরবিদায় দিয়ে এসে বিয়োগব্যথায় মুহ্যমান হলেও –সময়ের পদক্ষেপে তা ফিকে হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু মাটির মা–যাঁর সঙ্গে জীবনে ছাড়াছাড়ি হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই সেই মাকে হারানোর ব্যথা ভুলব কী করে? রাত্রিদিন অন্তরের অন্তস্তলে গভীর ক্ষতের অসহ্য যন্ত্রণা মনকে বিকল করে দিচ্ছে যেন। প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য-সম্পদ থেকে আমি নির্বাসিত। অপূর্ব সুষমামন্ডিত আমার ছেড়ে-আসা গ্রামের চরিদিকে শুধু সবুজের প্রাণভোলানো হাতছানি। সর্বত্রই ছিল সম্ভাবনার সুর, কিন্তু আগমনির বাঁশি বাজতে-না-বাজতেই যেন তা রূপান্তরিত হয়ে গেল বিদায়ের সুরে। সুন্দর ভুবন থেকে তো আমরা কোনোদিন বিদায় চাইনি, আমরা চেয়েছিলাম মানুষের মধ্যে বাঁচতে। কবিগুরুর বাণী তাই মনে আনত প্রেরণা। শহরের রুক্ষমলিন বাঁধন কাটিয়ে যখন আমার মাটির মায়ের স্নেহস্নিগ্ধ আবেষ্টনীর মধ্যে গিয়ে হাজির হতাম, তখনই কবিগুরুর মহাবাণীর সত্যতা সম্বন্ধে উপলব্ধি ঘটত। তখনই মন পাখা তুলে নেচে উঠত, মুখ দিয়ে অজান্তেই বেরিয়ে যেত, ‘মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই। মুহূর্তে ভুলে যেতাম শহরের সব গ্লানি, দুঃখকষ্ট, অপমান–জীবনের পুঞ্জীভূত দৈন্য অপসারিত হয়ে সেখানে বড়ো হয়ে দেখা দিত নবজীবনের গান। দু-পাশে ধানের খেতের রৌদ্র-ছায়ার লুকোচুরি খেলা, ভরা জোয়ারের জলে পরিপূর্ণ খালের মধ্য দিয়ে আঁকাবাঁকা পথের দু-পাশে ঘন সন্নিবিষ্ট নারিকেল বীথি আর সুপারিকুঞ্জের মনোরম খিলানের নীচে পল্লিমায়ের শুচিস্নিগ্ধ শান্তিনিকেতন। পল্লিমায়ের সেই মনোমুগ্ধকর ছবিখানি চোখ বুজে ধ্যান করলে আজও আমি তাকে স্পষ্ট দেখতে পাই। আজ সেই মাকে হারিয়ে নিজেকে রিক্ত ও সর্বহারা বলেই মনে হচ্ছে–জীবিকার্জনের ধাঁধায় শাহরিক যন্ত্রসভ্যতার চাপে শরীর ও মন ক্লান্ত হয়ে পড়লে আজও মাথা আপনাআপনি জন্মভূমির পায়ের ওপর লুটিয়ে পড়ে ভক্তি-নম্রতায়। আপন মনেই ভাবি মাটির মাকে কি ভবিষ্যতে আবার তেমনি আপন করে ফিরে পাব?
আমার ছেড়ে-আসা গ্রামও আর এককালের উদবাস্তু পুনর্বাসনেরই এক গৌরবজনক ইতিহাস। মগের উপদ্রবে অতিষ্ঠ হয়ে সাধকপ্রবর রামকৃষ্ণ ঘোষ একদিন জন্মভূমি ভাতশালা গ্রাম ছেড়ে আশ্রয়ের সন্ধানে অনির্দিষ্ট পথে নৌকা ভাসান এবং বসতি স্থাপনের উপযুক্ত মনে করে বরিশাল জেলার এই গাভা গ্রামেই আস্তানা পাতেন। সে আজ বহুদিনের কথা–তখন চারদিকে ধু-ধু দিগন্তবিস্তৃত বিল ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ত না এখানে। তারপর ধীরে ধীরে বহুযুগ পেরিয়ে এসে এই লোকবসতি বাংলার অন্যতম বৃহত্তম গ্রামে রূপান্তরিত হল–সাধক রামকৃষ্ণ ঘোষের বংশধরদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রামও উঠেছিল সমৃদ্ধির স্বর্ণশিখরে।
আমাদের পূর্বপাড়ার সঙ্গে পশ্চিমপাড়ার মিলনসেতু ছিল বড়ো পুলটা–বিলের শেষপ্রান্তে অস্তগামী সূর্য যখন অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় যেত দিগন্তের কোণে তখন এই পুলে বসত প্রাণচঞ্চল তরুণ আর কিশোরদলের মজলিশ। সময় সময় তাদের মধ্যে অসীম সাহসী কোনো যুবক হয়তো পুলের রেলিঙের ওপর থেকে ভরা বিলের জলে পড়ত লাফিয়ে। প্রবীণদের আড্ডা বসত দারোগাবাড়ির ঘাটলায়। পড়ন্তবেলায় মাঠে মাঠে ছেলেদের খেলাধুলা ও হইচই হট্টগোলে প্রাণবন্ত হয়ে উঠত সমস্ত গ্রামখানি। ভোরবেলা কিন্তু বাজারই ছিল আমাদের মহামিলন-ক্ষেত্ৰ-ছেলে-বুড়ো সবাই সেখানে এসে জুটত প্রাণের তাগিদে, গল্প করার নেশায়! ঘুম না ভাঙতেই বাজার বসত আমাদের গ্রামে–যার প্রয়োজন নেই সেও আসত সকলের সঙ্গে একজায়গায় ক্ষণিক মেলামেশার আনন্দ উপভোগ করতে। এ ছাড়া আর একটি মিলনক্ষেত্র ছিল গ্রামের পোস্ট অফিস। শহরের পোস্ট অফিসের মতো সেখানে কড়াকড়ি ছিল না–আর পোস্টমাস্টার, পিয়োন, ডাক-হরকরারা সবাই ছিল আপনজন, আত্মীয়-বিশেষ। পোস্ট অফিসের দরজায় বাংলায় ও ইংরেজিতে অবশ্য স্থায়ীভাবেই যথারীতি ‘ভিতরে প্রবেশ নিষেধ’ সংবলিত সাইনবোর্ডটি ছিল ফলাও করে টাঙানো! কিন্তু আমাদের গতি তাতে রুদ্ধ হত না কোনোদিন–চিঠি থাক বা না থাক সটান ঢুকে পড়তাম অফিসের ভেতর। সময় সময় মাস্টারমশায়ের কাজেও হাত লাগাতাম, শান্ত নিরীহ মানুষটি তাড়াতাড়িতে সব কাজ করে উঠতে হিমশিম খেয়ে যেতেন। তাঁর অবস্থার কথা চিন্তা করে আজও মনটা মুচড়ে ওঠে। কারও কোনো ভালো খবর পেলে তা নিজেই জানিয়ে আসার জন্যে অধীর হয়ে উঠতেন তিনি। জানি না আজ তিনি কোথায়, “সকলকে শুভসংবাদ দেওয়া যাঁর কাজ ছিল আজ তাঁর শুভসংবাদ দেবে কে?
গাভার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন দারোগাবাড়ির দৃশ্য ও তার বিরাটত্বের কথা,-পূর্ববঙ্গের বড়ো বড় জমিদারবাড়ির সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার স্পর্ধা রাখে এটি। খালের ধারে প্রকান্ড সুদৃশ্য ঘাটলা, নহবত, নবরত্ন মঠ–তার ওপরে স্থাপত্যশিল্পের কুশলী নিদর্শন, পুজোমন্ডপ, বিরাট বিরাট থামওয়ালা নাটখানা, লাইব্রেরি ইত্যাদি দেখলে দর্শককে বিস্ময়াবিষ্ট হতে হয়। এর পরেই সন্তোষের মহারাজা স্বর্গীয় সার মন্মথের দাদামশায় বাবু ঈশানের দালানের কথা বলা যায়। কত বিরাট আর উঁচু হতে পারে একতলা দালান এ তারই যেন একমাত্র দৃষ্টান্ত। সে একতলা কলকাতার তিনতলার সমান।
বর্ষাকালে আমাদের দেশে এঁটেল মাটির কাদা হয় খুব। পায়ের কাদা মাথায় ওঠে এবং ছাড়তে চায় না বলেই অনেকে এই কাদাকে বলেন ‘মায়া কাদা’! সত্যিই মায়া কাদা, তা না হলে সে কাদা আজও কেন তেমনি করেই মনের চারপাশে লেপটে আছে? হাজার চেষ্টাতেও উঠছে না সে-মাটি,-সে-মাটির মায়া কত তীব্র আজ দূরে বসে বুঝতে পারছি বেশি করে! ছোটোবেলায় বর্ষাকালে রাস্তার মাঝে মাঝে লম্বা লম্বা চারে (সাঁকো) পারাপার হতাম খাল। পরে গাভা সম্মিলনীর চেষ্টায় তা পাকা হয়েছে।
নেতাজি সুভাষচন্দ্রের পূতচরণের স্পর্শলাভ করে আমার গ্রাম ধন্য ও পবিত্র হয়ে আছে। হিজলি বন্দিনিবাসে পুলিশের গুলিতে নিহত শহিদ তারকেশ্বর সেনের চিতাভস্ম নিয়ে নেতাজি সেবার গৈলায় আসেন এবং বরিশাল পরিদর্শন করেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। খবর পেয়ে আরও দুজন বন্ধুর সঙ্গে গৈলায় গিয়ে চেপে ধরলাম—’সুভাষদা, আপনাকে গাভা যেতেই হবে।’ সে স্নেহের দাবি এড়াতে পারেননি তিনি। গ্রামে একটি শিল্পকলা ও কৃষি-প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা হয় সেসময়। সুভাষচন্দ্র সেই প্রদর্শনী উদবোধন করেন। সেবার তিনি আমাদের গ্রামের খদ্দর বয়ন প্রতিষ্ঠানটিও পরিদর্শন করেন এবং গ্রামের মধ্যে এমন একটি প্রতিষ্ঠান দেখে মুগ্ধ হয়ে তিনি বলেছিলেন–এই গ্রাম ও এই প্রতিষ্ঠান দুটোই যথার্থ বড়ো, আর আমরা তাঁর এই প্রাণখোলা উৎসাহ-বাণী পেয়ে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু আজ কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল! এক-একবার ভাবি, নেতাজি যদি এখনও ফিরে আসেন তাহলে আবার হারানো গ্রামকে, হারানো মাকে হয়তো ফিরে পেতে পারি।
ফুটবল খেলায় আমাদের গ্রাম একসময় ছিল শ্রেষ্ঠ–গাভার টিমের দাপটে বরিশাল জেলা কাঁপত ভয়ে। খেলা ছাড়াও নাম করার মতো ছিল আমাদের নিজস্ব থিয়েটার ক্লাব-পুজোর পর প্রতিবৎসরই থিয়েটার হত মহাসমারোহে। এই অভিনয়-প্রতিভাও জেলার গর্বের বিষয়। আমাদের থিয়েটার ক্লাব ছিল এমনি নামকরা। এ ক্লাবের অভিনয় দেখতে বানারিপাড়া, কুন্দহার, বাইসারি, নরোত্তমপুর, কাঁচাবালিয়া, নারায়ণপুর, ভারুকাঠি, রামচন্দ্রপুর, বীরমহল প্রভৃতি দূরাঞ্চল থেকেও বহুলোক আসত। গ্রামে যাত্রা হলে হিন্দু-মুসলমান সকলেই ভিড় করত-এক এক রাত্রে বিশ হাজার লোকের সমাবেশও দেখেছি। দেশ বিভাগের তিন-চার বৎসর আগে থেকে স্কুলবাড়ির উৎসাহী যুবক নির্মল ঘোষ পুজোর পর নিয়মিতভাবে তাঁর বাড়িতে তিন পালা করে যাত্রা ও সঙ্গে জারি গান দিতে আরম্ভ করেন এবং দেশ বিভাগের পরেও তা চলে আসছিল, কিন্তু এবারের শেষ ধাক্কায় সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে শুনেছি! যাত্রার সময় দেখেছি উৎসাহ মুসলমানদেরই বেশি। কুড়ি হাজার দর্শক হলে তার মধ্যে পনেরো হাজারই থাকত মুসলমান এবং তাতে স্থানীয় মুসলমান মাতব্বর ও মুসলিম স্বেচ্ছাসেবকরাই শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষারও ব্যবস্থা করতেন। গান না হলে মুসলমান ভাইরাই দুঃখিত হতেন বেশি, জিজ্ঞাসাবাদ এবং অভিযোগের অন্ত থাকত না তাঁদের।
ছেলেবেলার টুকরো টুকরো কত কথাই না মনে পড়ছে আজ! স্নানের সময় পুকুরে ডোবানো, ‘নইল-নইল’ খেলা, কৃত্রিম জলযুদ্ধের মহড়া, খালে নৌকাবাইচ প্রভৃতিতে সেসব ফেলে-আসা দিনগুলো ভরপুর। আনন্দের নির্যাসে পরিপূর্ণ ছিল আমার গ্রামের দৈনন্দিন জীবন। গ্রামে পুকুরের অভাব নেই, ছোটো-বড়ো পুকুর মিলে শ-পাঁচেক তাদের সংখ্যা। এসব পুকুরে স্কুল পালিয়ে ছিপ ফেলে লুকিয়ে মাছ ধরাও ছিল মস্ত একটা আকর্ষণ। জাল দিয়ে মাছ ধরার দিনে যে হইচই চলত আজও তা মনের চোখে স্পষ্ট দেখতে পাই। দু-চারটে বড়ো দিঘিও ছিল গ্রামে, তবে তাতে জলের চেয়ে দল-দামই জমে থাকত বেশি সময়, ওপর থেকে পুকুর বলে বোঝাই যেত না। এমনি একটা দিঘিকে জঙ্গল বলে ভুল করে একবার তাড়া খাওয়া এক চোর প্রায় ডুবতেই বসেছিল! দামের নীচে প্রায় দশ-বারো হাত জল থাকত সবসময়। ভবানী ঘোষের বাড়ির দরজার দিঘির পাড়ে দিনের বেলাতেই গা ছমছম করত–দিঘির পাড়ে তাল, তেঁতুল, গাবগাছের সমাবেশ সে-স্থানটিকে করেছিল আরও ভয়ংকর। শুনেছি আগে নাকি ওই দিঘির জলে চড়কের গাছ ফেলে রাখা হত এবং আর কেউ তার কোনো সন্ধান পেত না–কিন্তু চড়ক পূজার আগের দিন দিঘির পাড়ে এসে ঢাক বাজালে চড়কগাছ নিজে থেকেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠে পড়ত। গ্রামের মুসলমান পাড়ার শেষপ্রান্তে অবস্থিত ‘গুনা চোতরা’-র দিঘি সম্পর্কেও একইরকম অলৌকিক কাহিনি শোনা যায়।
ছোটোবেলার এক উত্তেজনাকর খেলা ছিল ঘুড়ির প্যাঁচ, অর্থাৎ ঘুড়ি ওড়ানোর প্রতিযোগিতা। এ নিয়ে বহু কলহ-বিবাদ হয়ে গেছে বন্ধুদের সঙ্গে! ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে দুর্ঘটনাও কম ঘটেনি–জীবনান্ত পর্যন্ত হয়ে গেছে। আমিও একবার সাক্ষাৎ যমালয় থেকে সসম্মানে এসেছি ফিরে। মাস ছয়েক ঝোলভাতের ব্যবস্থা করে দিয়ে ডাক্তার দাদু হেসেছিলেন আমার দুরন্তপনার কথা শুনে,–বাবা-মাও কম ভর্ৎসনা করেননি সেদিন। ঘুড়ি-লাটাই সেইদিনই দূর করে দিয়েছিলেন বাড়ি থেকে, অসহ্য ব্যথায় আমি পিটপিট করে শুধু দেখেই গিয়েছিলাম মর্মান্তিক ঘটনাগুলো! আজ মনে পড়লে হাসি পায়, ছোটোবেলায় ঘুড়ি-লাটাইকে কী দুর্মূল্য বস্তু বলেই না মনে হত! আর তা অন্য লোককে দান করে দেওয়ায় সেদিন যে দাগ লেগেছিল তার কোনো অর্থই আজ আর ভেবে পাই না। সে মন আজ অদৃশ্য, সামান্যকে অসামান্য করে দেখা যে কত কঠিন তা আজ বুঝতে শিখেছি। সে মন কী আমাদের সম্পূর্ণ মরে গেছে? এই ঘুড়ি ওড়ানোর মতো আর একটা ডানপিটে কাজ ছিল আমাদের–সে হচ্ছে অন্ধকার রাত্রিতে মজা করে ডাব পেড়ে খাওয়া। এর জন্যেও বহুলাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে আমাদের। ডাব-সমুদ্রের দেশেও ডাব চুরি করতে গিয়ে বকুনি খেয়েছি। অবশ্য এটা ঠিক চুরির পর্যায়ে পড়ে না–এটা ছিল অ্যাডভেঞ্চার এক ধরনের। এ খেলা তারুণ্যের দুঃসাহসিকতায় ছিল ভরা, যে দুঃসাহসিকতার নেশা আজকের দিনের জীবনকেও চঞ্চল করে তোলে মধ্যে মধ্যে।
আমাদের গ্রামে ব্রত-পুজো-পার্বণ লেগেই থাকত। তার মধ্যে দুর্গাপুজোটাই ছিল বিশেষরকম উল্লেখযোগ্য। লক্ষ্মীপুজোর মতোই ঘরে ঘরে হত দুর্গাপুজোর আয়োজন। একটা গ্রামে চল্লিশটি পুজো, সে কী কম কথা! পুজোর সময় গ্রামের চেহারাই যেত বদলে, সবার মুখে আনন্দের ছাপ। মহালয়ার দিন থেকেই হাটে-বাজারে সর্বত্র ভিড়–ছিমছাম ধোপদুরস্ত জামা-কাপড়ে সজ্জিত যুবকদের দেখে নির্জন গাভাকে এক নতুন শহর বলেই ভ্রম হত! যেসব ঢাকি বাঁধা ছিল তারা তো আসতই, উপরন্তু বাণারিপাড়ার বাজার থেকে আরও ঢাকি বায়না করে আনা হত উৎসবকে বেশি সজীব করে তোলার জন্যে। এই ঢাক বাছাই করা যার-তার দ্বারা হত না, এর জন্যে প্রয়োজন হত অভিজ্ঞ লোকের তৈরি কান! বাজনার সঙ্গে চমকদার নাচ দেখিয়েও ঢাকিরা খদ্দেরদের মন আকর্ষণ করত অনেক সময়। সেই ঢাকিরা বেশির ভাগই ছিল ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া অঞ্চলের মুসলমান। এরা সাধারণত ‘নাগারচি’ বলেই পরিচিত ছিল। পুজোর আর একটি জিনিস বেশি করে মনে পড়ছে, সেটি হল আরতি-আমাদের দেশে বলে ‘আলতি’। এই আলতি বরিশাল জেলারই একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আচার। পুরোহিতের আনুষ্ঠানিক আরতি শেষ হয়ে গেলে বাড়ির ও গাঁয়ের ছেলেরা এবং অনেক বাড়িতে ভাড়াটে ওস্তাদরা এই আলতি দিত। এক এক বাড়িতে রাত্রি কাবার হয়ে যেত, তবু শেষ হত না আলতি! সেরে সেরে ধুনো, গুগগুল ও ঝাঁকা ঝাঁকা নারকেল ছোবড়া পুড়ে ছাই হত। কতরকম কসরত ছিল এই অনুষ্ঠানে–একসঙ্গে দু-হাতে দুটো ধুপচি ও মাথায় একটা ধুপচি নিয়ে তান্ডবনৃত্য নাচলেও মাথার ধুপচি স্থানচ্যুত হত না দেখে আমি অবাক হয়ে যেতাম শৈশবে। যাঁদের বাড়িতে এসব পাট ছিল না তাঁদের ঢাকি গিয়ে যোগ দিত পাশের বাড়িতে। আলতির সময় ঢাকিদের চাঙ্গা রাখার কত প্রক্রিয়াই না ছিল–কতভাবে সিদ্ধির শরবত করে যে ওদের খাওয়ানো হত তার ইয়ত্তা নেই।
ধান-চালের দেশ বরিশাল জেলা, কাজেই সেখানে নবান্নের ঘটা যে একটু বেশি হবে তাতে আর আশ্চর্য কী! ধনী-দরিদ্র সকলেই সাধ্যানুযায়ী নবান্ন করত। অগ্রহায়ণ মাস ভরেই চলত এই নবান্নের আবাহন। পুজোর মতোই এ উপলক্ষ্যে বাড়ি ফিরতেন অনেক প্রবাসী লোক। নীল পুজোও আমাদের গ্রামে কম হত না। কয়েকদিন ধরে ‘বালা’-র নাচ, হরগৌরীর বিবাহের পালা, নানা ধরনের সং আর শোভাযাত্রা এবং শেষে ভোগ সরানো। চৈত্রসংক্রান্তির দিন দারোগাবাড়িতে মেলা বসত। সেই থেকে সমস্ত বৈশাখ মাস ধরেই গ্রামে মেলা চলত। ছেলে-মেয়ে, বউ-ঝি, চাকর-দাসী সকলেই এই মেলা উপলক্ষ্যে বাড়ির কর্তাদের কাছ থেকে পার্বণী পেত। মেলার সময়কার হাসিখুশি ছবিটির কথা মনে পড়লে আজও উন্মনা হয়ে পড়ি। সেদিনকার আনন্দের দিন কি আর কখনো ফিরে আসবে না মানুষের জীবনে? অত বড়ো গ্রাম আজ একেবারে ছন্নছাড়া শ্মশানভূমিতে পরিণত হয়েছে। শিবাদল শ্মশান জাগিয়ে শব-সাধনায় মেতেছে, এ মাতনের শেষ কোথায়?
আমাদের অঞ্চলটি সবদিক থেকেই বরিশাল জেলার একটি উন্নত এলাকা এবং আশপাশের ছোটো-বড়ো গ্রামগুলোও বাংলাদেশে কমবেশি পরিচিত। এসবের মধ্যে বাণারিপাড়ার কথাই সবিশেষ বলা যায়–গ্রাম হয়েও শহরের মর্যাদা তার। বন্দর এবং বড়ো হাট-বাজারের গঞ্জ হিসেবে তার প্রসিদ্ধি। পাশেই নরোত্তমপুরে রায়ের হাট নামকরা হাট। বাকপুর গ্রামে মাঘী সপ্তমীতে সূর্যমণির যে বিরাট মেলা বসত তার কথা সবারই জানা। আমাদের গ্রামের পাশেই মৌলবি ফজলুল হকের গ্রাম চাখারের অধুনা খুব উন্নতি হয়েছে। হক সাহেবের দৌলতে একটি কলেজও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এখানে–এ ছাড়া নতুন নতুন রাস্তা, সাব-রেজেস্ট্রি অফিস হওয়ায় গ্রামের চেহারা গেছে পালটে। আমাদের গ্রামের একদম লাগাও পূর্বদিকে ব্রাহ্মণ প্রধান বীরমহল গ্রাম, আর তা ছাড়িয়ে একটু এগিয়ে গেলেই কাঁচাবালিয়া ও রামচন্দ্রপুর। গাভার দক্ষিণ-পশ্চিমে বিল অঞ্চলে আটঘর ও কুড়িয়ানা গ্রাম দুটি নমশূদ্র-প্রধান। এ অঞ্চলের মাটিতে সোনা ফলে বলে প্রসিদ্ধি আছে। এখানকার শাকসবজি ও ফলমূল, বিশেষ করে আখ আর পেয়ারার সত্যি তুলনা হয় না। দীর্ঘ মাপের সোনালি রঙের আখ আর কাশীর পেয়ারার চেয়েও বড়ো পেয়ারা লুব্ধ করে যেকোনো লোকের মনকে! নমশূদ্ররা গ্রাম ছাড়বে না বলেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল, কিন্তু শুনলাম তারাও আটঘর ও কুড়িয়ানার মায়া ত্যাগ করে কোথায় যেন চলে গেছে।
ছুটির সময় যখন গ্রামে ফিরতাম তখনকার মানসিক অবস্থা বর্ণনা করা সম্ভবপর নয়– স্টিমার যেয়ে ভিড়বে স্টেশনে, সে পর্যন্ত দেরি সহ্য হত না প্রবাসী মনের। স্টিমার থেকেই চোখে পড়ত পল্লিমায়ের মনোমেহিনী রূপ! প্রথম সূর্যকিরণে বাসন্ডার জমিদারবাড়ির নবরত্ন মঠের চূড়া জ্বলত জ্বলজ্বল করে, খালের জলে পড়ত তার শতধা প্রতিচ্ছবি। ঘাটে বাঁধা থাকত জমিদারদের সবুজ বোট। চলার পথে একে একে উঁকি দিত বাসন্ডার স্কুল, বাউকাঠির হাট, পিপলিতার রায়ের বাড়ির দরজার মঠ, আরও কত কী! এসব অতিক্রম করলেই দেখা পেতাম গাভা স্কুলের–তখন মন বল্গাহীন, অপূর্ব হিল্লোলে হৃদয়তন্ত্রী উঠত নেচে। পটে আঁকা ছবির মতো পরিচ্ছন্ন আমার গ্রাম,-পূর্বের বাড়ির ‘রেন ট্রি’ গাছের কাছে নৌকো বেঁধে লাফিয়ে পড়তাম পল্লিমায়ের কোলে, শরীর স্নিগ্ধ হয়ে যেত তখন। তাড়াতাড়ি সোজা রাস্তায় লোকের বাড়ির মধ্য দিয়েই ছুটে যেতাম আমার কুটিরে–যেখানে জন্মভূমির সঙ্গে জননীর স্নেহের পরশ ছিল মিশে। তাঁদের দ্বৈত স্নেহে আমি ধন্য হয়েছি একদিন, কিন্তু আজ? সেসব আকর্ষণী শক্তি কোথায় গেল? নিজের গ্রামে যাওয়ার কথাও ভাবতে পারি না কেন? সব কিছু হারিয়ে কেন আমরা সর্বহারা উদবাস্তু হয়েছি? স্বাধীনতার জন্যে? সে-স্বাধীনতা কোথায়? আবার কবে আমার জন্মভূমির কোলে ঠাঁই পাব, তার দিন গোনা ছাড়া উপায় দেখছি না কিছু। মনকেই প্রশ্ন করছি বারবার–মায়ের ডাকে আবার আমরা মিলব কবে? কবে মায়ের পায়ে আবার মাথা ঠেকাবার সৌভাগ্য হবে?
.
কাঁচাবালিয়া
জল–জল–জল, চতুর্দিক জলে ভরতি। মনোরম সরসতা। জল দেখে চিত্ত বিকল হয় না, আশা জাগে, মন ভেসে যায় সাতসমুদ্দুর তেরো নদী পারের নারকেল-সুপারিঘেরা, সবুজ দারুচিনি দ্বীপের প্রাণমাতানো পল্লিমায়ের কাছে! শুষ্ক রুক্ষ শহরের বুকে বসে আজ বেশি করে মনে পড়ছে আমার জননী জন্মভূমির কথা, আমার সোনার বরন কাঁচাবালিয়াকে। আজ আর তার সোনার রং নেই, পুড়ে কালো বিবর্ণ হয়ে গেছে। মানুষের লোভ, মানুষের স্বার্থ, ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব তার গৌরবময় ঐতিহ্যের গায়ে কালি ছিটিয়ে দিয়েছে। আমাদের বর্বরতা, আমাদের কলঙ্ক, আমাদের বিরোধ সমস্ত কিছু সৎপ্রচেষ্টারই ঘটিয়েছে অবসান। যে দেশের বাতাস টেনে নিয়ে এত বড়োটি হয়েছি, যে দেশের ধুলোয় উঠেছে শরীর গড়ে, যে দেশের খাদ্য জুগিয়েছে শক্তি, সেই দেশকে আমরা আর নিজের জন্মভূমি বলতে পারছি না ভেবে বুক ফেটে যাচ্ছে অসহ্য ব্যথায়! আজকের এই হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর বুকে কে শান্তির বারি সিঞ্চন করবে জানি না, পৃথিবীর উত্তপ্ত বুকে কে শীতলতা বইয়ে দেবে তার সন্ধানই করছি শত দুঃখকষ্টকে অগ্রাহ্য করে দেশ-দেশান্তরে ঘুরে ঘুরে। কবে দেখা পাব আমরা সেই মহামানবের, কবে বলতে পারব রবীন্দ্রনাথের মতো–’ওই মহামানব আসে, দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে?’
শরীরে শিরা-উপশিরার যেমন কাজ রক্ত চলাচলে সহযোগিতা করা, তেমনি নদীর কাজ দেশের বুকে ফসল ফলাবার। মানুষকে বাঁচিয়ে রাখবার কাজে নদীই প্রধানতম সহায়, তাই আমাদের গ্রামখানি ছিল এত সজীব, এত সৌন্দর্যের প্রতীক। জালের সুতোর মতো অসংখ্য খাল-বিল দিয়ে জোয়ারের জল আসত জীবনের জোয়ার নিয়ে। খালের প্লাবন ধ্বংসমুখী হয়ে কোনোদিন কাঁচাবালিয়ার বুকে দেখা দেয়নি, সেখানে নদী বর্ষাকালেও গ্রাম প্লাবিত করে যেমন মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করে না, তেমনি আবার শীতকালেও জলের অভাব ঘটিয়ে মানুষকে নাকের জলে চোখের জলে করে ছাড়ে না। উত্তর অঞ্চলের গোঁয়ার নদীর মতো দুষ্ট আমাদের গ্রামের নদী নয়, সে মানুষের মতোই মানুষের দুঃখ-কষ্ট বোঝে, মানুষের সুখদুঃখের মধ্যেই নিজেকে জড়িয়ে রাখতে চায় সে গৃহস্থ বধূর মতো! আমার গ্রামবাসীরা সেদিক থেকে ছিল সত্যি ভাগ্যবান। অধ্যাপক হেম গুহ তাই মাঝে মাঝে রসিকতা করে নদীটিকে আহ্বান জানাতেন ‘ভেনিস সুন্দরী’ বলে!
যথার্থ নাম হয়েছিল এই ‘ভেনিস সুন্দরী’। ঝরঝরে, তকতকে, পুণ্যতোয়া ব্রীড়াবনতা শান্ত নদীর অন্য কোনো নাম যেন মানায়ই না। নারকেলকুঞ্জ, সুপারির বাগান, আম-কাঁঠাল কদলীগুচ্ছের ধারে ধারে বাঁশবন-ঘেরা সুদৃশ্য সব বাড়ি–কুড়ি-ত্রিশ হাত পরিসর খাল চলে গেছে এঁকে-বেঁকে সুতোর মতো সমস্ত বাড়িকে স্পর্শ করে। আবার কোথাও কোথাও পরিখার আকার ধারণ করে বেষ্টন করেছে গোটা গ্রামকে। সীমার মধ্যে অসীম হয়ে ওঠার সাধনাই যেন তার প্রধান সাধনা। এ হেন উত্তর বরিশালের মধ্যমণি ছিল আমার ছেড়ে-আসা গ্রামখানি। বঙ্গজ কায়স্থ প্রধান কাঁচাবালিয়ার সীমানা ছিল এক মাইলেরও কম, কিন্তু তাতেই সে কখন গড়ে তুলেছিল তার নিজের ঐতিহ্য। সৌন্দর্য সাধনার ক্ষেত্রে সে হয়ে উঠেছিল মহিমময়ী, মহীয়সী!
প্রবাদ আছে, সম্রাট শাজাহানের রাজত্বকালে দক্ষিণের মগ-অত্যাচারের হাত থেকে প্রাণ মান-ইজ্জত রক্ষার জন্যেই গুহ আর বসু বংশীয়েরা চলে এসে বসতি স্থাপন করেন এখানে। চন্দ্রদ্বীপের ভূঁইয়া কন্দর্পনারায়ণের আশ্রয়ে পার্শ্ববর্তী গাভা, নরোত্তমপুর, বাণারিপাড়া, উজিরপুর, খলিসাঁকোটা প্রভৃতি গ্রামে দেখতে দেখতে বিরাট সভ্য সমাজ গড়ে উঠল। ইংরেজ আমলের মাঝামাঝি এসে এঁদের অনেকেই কৌলিন্যের খোলস ত্যাগ করে ছোটো ছোটো নৌকো নিয়ে বেরিয়ে পড়েন জ্ঞান ও অর্থের উৎস সন্ধানে। তাঁদের কেউ কেউ যান ঢাকায়, কেউ কেউ সরাসরি কলম্বাসের মতো পাড়ি দেন কলকাতা মহানগরীতে! সেকালে ম্যাট্রিক এবং ছাত্রবৃত্তি পাস করে অনেকে ডাক্তারি লাইনেও গিয়েছিলেন। চিকিৎসাজগতে গিয়ে সুনাম প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে কটকের জেলা অধিকর্তা মণীন্দ্র গুহের পিতা কীর্তি স্থাপন করেছেন। সে-সময় পদ্মা নদী এত বিপুলকায়া হয়ে ওঠেনি। সবে রাজা রাজবল্লভের কীর্তিনাশ করতে আরম্ভ করেছে। আমার পূর্বপুরুষগণ দেখেছেন সেই কীর্তিকে গ্রাস করেছে কী করে কীর্তিনাশা পদ্মা। প্রতিমার চালচিত্রের মতো ধীরে ধীরে ডুবে গেছে সেই সভ্যতা, সেই সংস্কৃতি, সেই বীর্যবান পুরুষের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। ভাবলেও শিহরন জাগে শরীরে– সেইদিনকার মতোই কি আমাদেরও কীর্তিনাশ হল না আজ? আজকের মতো অসহায়তা নিয়ে সেইদিনের বুকেও কি দুঃখের বুদবুদ ওঠেনি মানবমনে?
কিন্তু সেই শ্মশানের মধ্যে থেকেই আলো উঠেছে জ্বলে। সভ্যতার মৃত্যু নেই, সভ্যতার মধ্যেই মানুষ থাকবে বেঁচে। ধ্বংসস্তূপের মধ্যেই আবার গড়ে উঠল রাস্তাঘাট, পুকুর, দালান, টিনের কোঠা, পাকা দালান–আবার গ্রাম শ্রীমন্ডিত হল রাজবল্লভের বংশধরদের আপ্রাণ চেষ্টায়। প্রাণের বাতি জ্বালালেন গ্রামে গ্রামে, আবার মানুষের মুখে ফুটল হাসি, গান, গল্প। মানুষ আবার মানুষ হল!
সেই হাসিগানের রেশ মেলাতে না মেলাতেই আবার নেমে এল বিপদের কালো যবনিকা, শঙ্কিত মানুষ দিশেহারা হয়ে প্রাণভয়ে ছুটল দেশ-দেশান্তরে! কেন এমন দুর্ভাগ্য নেমে আসে বারবার লাঞ্ছিত মানুষের ভাগ্যে? মগের অত্যাচার থেকে জীবন বাঁচাতে একবার আমাদের দেশত্যাগী হতে হয়েছিল–আবার দেশত্যাগে বাধ্য হলাম বিংশ শতাব্দীর হিংস্র বর্বরতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে! ইতিহাস আমাদের ভাগ্যে কী লিখেছে জানি না,–আজ শুধু তার নির্মম রসিকতাটুকুই উপভোগ করছি সর্বস্ব খুইয়ে নতুন ইহুদির পর্যায়ে নেমে এসে! ভারত-পাকিস্তানের সংখ্যালঘু মন্ত্রীদ্বয় সেদিন বানারিপাড়া গিয়ে নিশ্চয়ই দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন হিন্দু-অধ্যুষিত গ্রামের শ্মশানশ্রী দেখে! দেখবার সময় তাঁদের একবারও কি মনে হয়নি সেই কাম্বোডিয়ার সুষুপ্তা সুন্দরী বা Sleeping Beauty-র উৎসভূমির এমন বৈধব্য-মলিন চেহারা কেন হল? কোথায় গেল তার সৌন্দর্য? কোথায় গেল সেই পূর্বস্মৃতির রুপালি রূপ। শতবর্ষ আগে ভয়াবহ ওলাওঠা যা করতে পারেনি, সর্বনাশী ৭৬-এর মন্বন্তরে দেশের যে হাল হয়নি, ১৩৫০-এর নাগিনির দীর্ঘশ্বাস যে গ্রামের অঙ্গে কালির কলঙ্ক লেপে দিতে পারেনি, সেই অভাবিত সর্বনাশ কেন হল স্বাধীনতা লাভের মাত্র আড়াই বছরের মধ্যে? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ। কিন্তু মানুষ কি আজ আর মানুষের পর্যায়ে আছে? মানুষ কেন মানুষকে আজ সাপের মতো ভয় করছে? জানি মানুষের ওপর বিশ্বাস ফিরিয়ে আনাই আজকের যুগের প্রধানতম সংগ্রাম! সেই সংগ্রামে জয়ী হব আমরা–হে ঈশ্বর, শক্তি দাও আমাদের মনে! আমরা অমৃতের পুত্র–বিষক্রিয়া আর কতদিন কাজ করবে আমাদের ভেতর?
বাইশ-শো লোকের গ্রাম ছিল কাঁচাবালিয়া। তার বাসিন্দাদের অধিকাংশই ছিলেন ব্যবসায়ী, সুচিকিৎসক, সুবিচারক, কৃতী অধ্যাপক, নামজাদা শিল্পী এবং সংগীতজ্ঞ। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ অর্থোপার্জনের জন্যে বাইরে বাইরে কাটালেও জন্মভূমিকে তাঁরা ভোলেননি একদিনের জন্যেও। তাঁদের আন্তরিক টান গ্রামবাসীকে মুগ্ধ করত! মনে পড়ে, পুণ্যতোয়া নদী হিমালয়ের গাত্র ধৌত করে পলিমাটি সঞ্চয়ের কাজ সমাপ্ত করত যখন, তখন শুভ্র শরতের হত উদবোধন। লক্ষ করেছি সেই শারদপ্রাতে শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে ছুটে আসতেন তাঁরা এই নদীমাতৃক জন্মভূমির পায়ে হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধাভক্তির অর্ঘ্যদানের জন্যে। আজ ইচ্ছে থাকলেও মায়ের কাছে ছুটে যাওয়ার উপায় নেই আমাদের। আমরা এখন পরবাসী, অবাঞ্ছিতের দল। তা ছাড়া সেই জল, সেই হাওয়া কোথায় আজ?
মনে পড়ছে আজ বেশি করে মজিল সাহেবের কথাগুলো! আমাদের দেশ ছাড়া হতে দেখে তিনি একদিন বলেছিলেন—’আপনাদের ভয়টাই বড়ো বেশি।’ স্বীকার করতে মনে বেধেছিল তাঁর অভিযোগটি। আমরা ভীত নই, আমরা কাপুরুষ নই, আমরা দুর্বল নই। আমরা অযথা হানাহানি, রক্তপাতে অসহায় বোধ করি। এই সেদিনও আমাদের গ্রামের ছেলেরা বর্শা দিয়ে বাঘ শিকার করেছে। মাত্র ৩০ বছর আগে আমাদেরই বুটকিন সরকার একখানা খাঁড়া দিয়ে একসঙ্গে দুটো বাঘ ঘায়েল করেছিল। এগুলো গালগল্প নয়, দিনের আলোর মতোই সুস্পষ্ট। তবুও মজিল সাহেবের কথা শুনে চুপ করেই থাকতে হল। তর্ক করে গায়ের শক্তি প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করে কী হবে আর? আজও তো কিছু মেয়ে-পুরুষ রয়েছে সেখানে, তাদের মনোবল প্রশংসা করার মতো। সেই শূন্যপুরীতে এখনও যে কেউ কেউ ফিরে যায় তা কি শুধু দুটো ফলের জন্যে, না, অকৃত্রিম প্রাণের টানে?
শহিদ সাহেব আসবার সময় জানিয়েছিলেন—’আপনাদের রক্ষা করলাম, আর আপনারাই আমাদের এভাবে ছেড়ে যাচ্ছেন? এসব কি ভালো করছেন মশায় আপনারা? এখান থেকে এমনভাবে দলে দলে গেলে সিকি লোক মরবেন শুধু না খেতে পেয়ে, গুণ্ডায় মারবে সিকি, আর বাকি লোক মরবেন শীত-গ্রীষ্ম-অনাহারে। এরই পিঠ পিঠ অবশ্য বলেছিলেন গম্ভীর হয়ে কেটে কেটে—’আমরা মসজিদে মোনাজাত করার সময় খোদার কাছে প্রার্থনা করেছি এই বলে,-খোদা, আমাদের প্রতিবেশীদের যেন কোনো অনিষ্ট না হয়। তারা সুখে থাকুক, শান্তিতে থাকুক।’ শহিদ সাহেবের কথা আজও কানে বাজছে। তাঁর প্রার্থনা খোদার কানে গেছে কি না জানি না কিন্তু এমন দরদি মনের পরিচয় পেয়ে সেদিন চোখ দিয়ে আমার কৃতজ্ঞতার জল ঝরে পড়েছিল।
কিন্তু সুবিধাবাদী চ্যাংড়ার রূপ সর্বত্রই এক। ওখানেও তার ব্যতিক্রম নেই। আমাদের মধ্যে যখন এই ধরনের হৃদয়াবেগের কথা হচ্ছিল ঠিক সেই সময় এসে হাজির হল আসমান। খানিকক্ষণ হাঁফ ছেড়ে সামনের চেয়ারটায় বসে দু-বার লাঠি ঠুকে অকস্মাৎ প্রশ্ন তোলে-‘কী কইছ মেয়ারা? আমাগো পাকিস্তান ছাইড়্যা মহায়রা এরকম যায় কা?’ তারপর একটা চোখ ছোটো করে আমার দিকে তাকিয়ে নিম্নকন্ঠী ষড়যন্ত্রীর মতো বলে—’হুনছি কিছু ব্যাচোনের আছে? বাড়িডা বোলে ব্যাচবেন?’ তার কথা শুনে আমরা সবাই তাজ্জব বনে গিয়েছিলাম। ছোকরা বলে কী, বাড়ি কেনার টাকা হল কোথা থেকে ওর?
কথাটা যাচাই করার জন্যে মজিল সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—’এই আপনার দল? এরাই আমাদের রক্ষা করবে বিপদ-আপদের মধ্যে?’ কাঁদো কাঁদো হয়ে ম্লানমুখে মজিল সাহেব শুধু জানালেন–সবই বুঝি ভাই, একটা কথা কী জানেন? এমনিভাবে হিন্দুরা গ্রাম ছেড়ে চলে গেলে আমরা কাদের নিয়ে থাকব বলুন? আপনাদের সঙ্গে একত্রে এতদিন বসবাস করার পরেও যদি অনাত্মীয়ের মতো আমাদের ছেড়ে যান তাহলে তার চেয়ে বড়ো সর্বনাশের কথা আর কী হতে পারে! এরা শিশু, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করার বুদ্ধি কোথায় এদের? পাপের আপাতমধুর স্বাদেই বিভোর হয়ে রয়েছে এরা, এদের কথার তাই দাম নেই কিছু। সমস্ত হিন্দু গ্রাম ছেড়ে গেলে হিন্দুর মনে যেরকম কষ্ট লাগে, আমাদেরও সেই একইরকম কষ্ট হয়। লক্ষ করেছি কথা বলতে বলতে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছিল তাঁর চোখ বেয়ে। জানি না মজিল সাহেবের সাঙ্গোপাঙ্গরা তাদের হিন্দুভাইদের অভাব অনুভব করেন কি না আজও, কিন্তু আমরা দু-বেলা স্মরণ করি তাঁদের অশ্রুরুদ্ধ নয়নে। আজ তাই বারবার মনে পড়ছে মজিল সাহেব আর শহিদ সাহেবের কথা। কিন্তু গ্রাম ছাড়ার সময় তাঁরা আরও নিবিড় করে বাধা দিলেন না কেন? কেন তাঁরা প্রাচীর তুলে দিলেন একই মায়ের বুকের ওপর? এ সর্বগ্রাসী দুঃখ তো ভবিষ্যতের হিন্দু-মুসলমান মানবে না। এ যে সকলকেই নিষ্ঠুরভাবে দলন করে চূর্ণ করে দেবে! তবে দুঃখী মানুষ আজও কেন জাতিভেদের জাঁতাকলে পড়ে পিষ্ট হচ্ছে অকারণ? কেন তারা বিদেশি চক্রান্তের ক্রীড়নক হয়ে নিজের সর্বনাশ নিজে করছে আহাম্মকের মতো? এ প্রশ্ন কাকে করি? কে উত্তর দেবে? পাকিস্তান থেকে মজিল সাহেবও কি এমনি চিন্তাই করছেন আজ?
এমন সোনার দেশ কি কারও ছাড়তে ইচ্ছে হয়? প্রথম প্রথম ভীত মানুষ যখন দু-একজন করে ঘরবাড়ি বিক্রি করে দিয়ে চলে আসতে শুরু করে তখনও প্রমদা ঠাকরুন গৃহনির্মাণ ও উদ্যানরচনায় ব্যস্ত। দেশে এমন দাবানল জ্বলে উঠবে কে চিন্তা করেছিল? ভাইয়ে ভাইয়ে কোন্দল হয়, আবার মিটেও যায়, কিন্তু সেদিনের সামান্য ফুলকিই যে দেশজোড়া তান্ডবের সৃষ্টি করবে তার হদিশও সামান্য মানুষ পায়নি! প্রমদা ঠাকরুন মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, গ্র্যাজুয়েট পুত্রবধূ এনেছিলেন ঘরে। নিজে লেখাপড়া তেমন না জানলেও বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা ছিল তাঁর আন্তরিক। সেই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি খাটতে পারতেন অসম্ভব। নিজের হাতে বেঁধে তিনি কত ভোজ নামিয়ে দিয়েছেন গাঁয়ের। জানি না তাঁর সাজানো বাগান আজ শুকিয়ে গেছে কি না!
সোনালি ভবিষ্যতের কথা তুলত মাঝে মাঝে কচি মেয়ে কল্যাণী। সে আবদার করত, আমাদের গ্রামের এই কাঠখোট্টা নামটা পালটে কাঞ্চনবালা রাখলে হয় না? হিন্দুরা যেমন সবাই লিখতে-পড়তে জানে, মুসলমানরাও সেইরকম লিখতে-পড়তে শিখবে কবে? ওরা সবাই কেন হিন্দুর মতো স্কুলে যায় না, জ্যাঠামশায়? এমনি কত অদ্ভুত অদ্ভুত কথার স্মৃতি ভিড় জমাচ্ছে আজ মনের আকাশে। আজ সে অনেক বড়ো হয়েছে, আমাকে দেখতে এসে সেদিনও বলে গেছে, এখন আর গ্রামের ক-বিঘে জমিই আমাদের বাড়ি নয় জ্যাঠামশাই, এখন আমাদের বাড়ি সমগ্র ভারত জুড়ে!’ কল্যাণী এত দুঃখেও ভেঙে পড়েনি, সে যেন বিরাটত্বের স্বাদ পেয়েছে।
অশীতিপর বৃদ্ধ সাবডেপুটি দেবেনবাবু সমস্ত কাজ ফেলে পুজোর সময় দেশে আসতেন ছুটে। তিনি না এলে মা আসবেন কী করে? তাঁর আসার পরদিন থেকেই শুরু হত আগমনি সংগীত। ভিখারি-বাউলরা সাবডেপুটি বাবুর চারপাশ ঘিরে আরম্ভ করে দিত গান,
আসছেন দুর্গা স্বর্ণরথে
কার্তিক গণেশ নিয়ে সাথে।
আসছেন কালী পুষ্পরথে
মুন্ডমালা নিয়ে গলে।।
দুর্গাপুজোর ধুমধাম যেন আজও জ্বলজ্বল করছে চোখের সামনে। কী হইহুল্লোড়ের মধ্যে দিয়ে কেটে যেত দিনগুলো তা চিন্তা করেও আশ্চর্যবোধ হয় আজ। আজ একটি দিন কাটতে চায় না, দুঃখের জীবনপৃষ্ঠা ওলটাতে যে এত বিলম্ব হয় তা কে জানত আগে! কিন্তু সেদিন সারারাত জেগে রামায়ণগান শোনার উৎসাহ পেতাম কোথা থেকে! আনমনা হলেই সেইদিনকার রামায়ণগানের টুকরো টুকরো কথাগুলো বেরিয়ে পড়ে অজান্তে শত দুঃখকষ্টকে অগ্রাহ্য করে,
অযোধ্যানগরে আজ আনন্দ অপার
রাম রাজ্যেশ্বর হবে শুভ সমাচার।
পল্লব কুসুমহারে কিবা শোভা দ্বারে দ্বারে
প্রতি ঘরে সবে করে মঙ্গল আচার।
মধুর মঙ্গল গীত শুনি অতি সুললিত
বাজনা বাজিছে কত বাজে অনিবার।।
চোখের সামনে স্বচ্ছ হয়ে উঠছে আনন্দমুখর দিনগুলোর কথা। প্রতি ঘরে ঘরে যাদের আনন্দধ্বনি জাগত তাদের ঘরে আজ মর্মরধ্বনি কেন জাগছে? আলোকের ঝরনাধারায় কি এই দুঃখকষ্টকে ধুয়ে ফেলা যায় না আমাদের জীবন থেকে?
এমনি কত শত দুঃখের পাঁচালি মনটাকে করছে ক্ষতবিক্ষত। কোন দুষ্টু ছেলে আমাদের ঢিলের মতো চক্রাকারে ভারতময় ছিটিয়ে দিল? রোহিণী কবরেজমশায়ের ছোটো শিশির স্বর্ণপটপটি আজ গড়াতে গড়াতে এসেছে হাবড়ায়! সারাজীবনব্যাপী শ্রমের ফল, কত বাড়ির জনশূন্য ছবি হয়তো দেখছেন গোপাল দে মশায় বর্ধমানের ঘোলাটে আকাশে! জানকী দাসের লেকচার স্তব্ধ হয়ে গেছে শিয়ালদা প্ল্যাটফর্মের পূতিগন্ধময় পরিবেশে! অত বড়ো বাড়ির মালিক হেমন্ত গুহ সোনার পুতুলি পুত্রকন্যার হাত ধরে এসে মাথা গুঁজেছেন অন্ধকার ক্যাম্পে। তাঁর পঞ্চাশ খন্ড ইংরেজি বিশ্বকোশের পাঠক আজ কারা? কার্ভালোর দামি চকচকে পোশাকটা কী আজ ‘ভবের কোলায়’ (বড়ো মাঠে গড়াগড়ি যাচ্ছে? নরেন বসু উকিল হয়তো থিয়েটারের শখ মেটাচ্ছেন রাঁচিতে! তাঁর সিরাজ আজ চমকে চমকে উঠছে স্বপ্নের মধ্যে আগুন-রক্ত-তরবারি কিংবা বর্শা দেখে!
ভোলা যায় না, ভোলা যাবে না আমার লাঞ্ছিত জন্মভূমিকে। সেই সঙ্গে ভোলা যাবে না বিরাশি বছরের বৃদ্ধ শশী ঠাকরুনের চশমা এঁটে চিঠি পড়ার দৃশ্যকে, ভোলা যাবে না দামোদর বসুর সূক্ষ্ম হিসেব-বিলাসী মনকে, ভোলা যাবে না সাধু ভাষার ধ্বজাধারী ঈশ্বর বসুকে। তিনি সাধুভাষা প্রয়োগ করতেন স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করার সময়েও। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথোপকথনের টুকরো কথাগুলো মনে পড়লে আজও হাসি পায়। একবার সামান্য কলার পাতা ছেঁড়ার জন্যে ঈশ্বরবাবু স্ত্রীকে কড়া তিরস্কার করে বলেন—’এত কষ্টে আনীত, ভাদুসার হইতে কদলীবৃক্ষ, তার পত্র ছিন্ন, কে না হয় বিষণ্ণ?’ বলেই পত্নীর পিঠে সপাং সপাং করে বেত্রাঘাত!
মনে পড়ছে গ্র্যাজুয়েট বর দেখতে গিয়ে এই গ্রামেরই একজন পাত্রের হাতের লেখা চেয়েছিলেন দেখতে। এমন কত শত কাহিনি মনকে উতলা করছে কেন জানি না। যাঁরা মনের অতলে গিয়েছিলেন তলিয়ে তাঁরা সবাই উঁকি দিচ্ছেন একের পর এক। তাঁরা সবাই কোথায় আজ? মনে মনে তাঁদের স্বাস্থ্য, অর্থ, শান্তি কামনা করছি। তাঁরা সুখে থাকুন, ভালো থাকুন।
শুনেছি আমার গাঁয়ে আর পুজো হয় না, নবান্নের ধুম নেই। মানুষহীন গ্রাম শ্বাপদসংকুল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবার কি কোনোদিন ছেলেরা ভোরে উঠে কাক ডাকবে–’কাউয়া কোকো কো, আমাগো বাড়ি আইয়ো’ বলে? পৌষ সংক্রান্তির আগে কৃষক-মজুররা আর কি গৃহস্থের বাড়ি এসে–”রাজার বাড়ি আইলাম রে!’ বলে দাঁড়াবে? কুমির আর বাঘের পুজোর সঙ্গে রসের পিঠে, চিতে পিঠে খাওয়া হবে আর কোনোদিন?
মনুষ্যত্বের অবমাননা পৃথিবীতে এমন ভীষণভাবে আর কোনোদিন হয়নি, তবুও দুঃখকষ্ট অপমান নির্যাতনের মধ্যে মানুষ অমৃতলাভ করবেই। পাঁচশো বছর আগে তুরস্কের রাজধানী থেকে বিতাড়িত গ্রিক খ্রিস্টানরা পশ্চিম ইউরোপে জ্বেলেছিলেন প্রজ্ঞা ও শান্তির নতুন আলো। সেই আলোয় সমগ্র ইউরোপ আজ হয়ে উঠেছে আলোকিত; অত্যাচারী তুরস্কের পরাজয় হল বিতাড়িত বিধর্মীদের কাছে। মনে হয় বাংলার কাজ হবে নতুন আলোকবর্তিকা হাতে এগিয়ে যাওয়া–সমগ্র দেশের প্রাণে নতুন জীবন যোজনা করা। জানি ভারতের জয় অবশ্যম্ভাবী। ছোট্ট জমির মালিক আর আমরা নই, এখন সারাভারতবর্ষ আমাদের মাতৃভূমি। আমাদের সাধনা এখন বিরাট হওয়ার, মহৎ হওয়া প্রাণ-গঙ্গার ঢেউ একদিন ঐরাবতের মতো সমস্ত বাধবিপত্তিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবেই, নতুন পরিবেশে আবার আমরা সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়াব, আবার আমরা মানুষ হব।
.
মাহিলাড়া
বরিশাল থেকে মাদারিপুর ছত্রিশ মাইল দীর্ঘ যে প্রশস্ত সরকারি রাস্তাটা চলে গেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে–তারই মাঝামাঝি জায়গায় আমাদের জন্মভূমি মাহিলাড়া গ্রাম। গ্রামটি রাস্তার পুব ধারে। এরই প্রায় একমাইল দক্ষিণে রাস্তা-সংলগ্ন গ্রাম বাটাজোড়, স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের পৈতৃক বাসভূমি। সরকারি রাস্তার সঙ্গে সঙ্গে বয়ে চলেছে সরকারি কাটা খাল।
মায়ের কোলে যেমন শিশুর সুখের সীমা নেই, তেমনি সুখ ছিল আমাদের পল্লিমায়ের কোলে। সরকারি খাল থেকে আর একটা খাল পুব দিকে তিন ক্রোশ দূরে গিয়ে মিশেছে আড়িয়ালখাঁ নদীতে। এই খালের দুই তীরে ছবির মতো গ্রাম মাহিলাড়া। জোয়ার-ভাটায় খালের জল সদাই চঞ্চল, যেন পল্লিমায়ের বুকে দুলছে একছড়া কণ্ঠহার! ভোরে যখন সূর্য ওঠে, পূর্ণিমায় যখন নীল আকাশে চাঁদ ফোটে, তখন খালের জলে লক্ষ মানিক জ্বলে।
মাঝখানে একটা কাঠের পুল এক করে দিয়েছে এপার-ওপার। পুলের উত্তরে একটা বহুপ্রাচীন তালগাছ, আর দক্ষিণে একটা কদমগাছ। আষাঢ়ে সবুজ পাতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ফোটে রাশি রাশি কদম ফুল। এরা সজল চোখে হাসি ফুটিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখে। খালের দু-ধারে আরও কত গাছ–হিজল, জারুল কাঁঠাল। জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন প্রথম জোয়ারের জল ছুটে আসে কূল ছাপিয়ে, তখন তাতে ভাসে রাশি রাশি হিজল আর জারুল ফুল। হিজল ফুল লাল, আর জারুল ফুল বেগুনে। অজস্র ফুল পরস্পর মিলেমিশে রঙিন কার্পেটের মতো ভেসে আসে জোয়ারের জলে, আর পিছিয়ে যায় ভাটার টানে–নদীর দিকে।
গ্রামের উত্তরে খানিকটা দূরে শ্মশ্রুবহুল ঋষির মতো দুটো বটগাছ। বিশাল ছায়া ফেলেছে। পায়ে-চলা পথের ওপরে। কত বয়স তাদের হল কে তার হিসেব রাখে। পূর্বসীমায় গুপ্তদের দিঘির পাড়ে একটা বকুল গাছ। ফুল ঝরে পড়ে তার দিঘির জলে। দক্ষিণে সরকারের মঠ। তিন-চারশো বছরের পুরোনো দেউল। তার দেহে ঢেউ খেলানো কারুকাজ। আর একটু পশ্চিমে একটা অশ্বত্থাগাছ–বুঝি হাজার বছর বয়স হবে তার। এটি গোবিন্দ কীর্তনীয়ার গাছ বলে জনশ্রুতি। কী প্রকান্ড দশদিকে ছড়ানো এর ডালপালাগুলো। ওখানে নাকি কোনো দেবতার বাসা। কেউই চড়ে না ওই গাছে। আর একটা পুরোনো মন্দির গাঁয়ের ঠিক মাঝখানে–ওই সরকারের মঠের সমবয়সি। এরও সর্বদেহে খোদাই-করা পদ্মফুল, লতাপাতা! ওই মন্দিরে দুর্গাপুজো হয় প্রতি আশ্বিনে। গ্রামের পশ্চিম সীমায় সরকারি রাস্তায় একপ্রান্তে সুদীর্ঘ আর সুবিশাল শিমুল গাছ–শালপ্রাংশু মহাকাল। ফাগুনে আগুন-বরন ফুল ফুটিয়ে চেয়ে থাকে ও আকাশের দিকে। এই চতু:সীমার বাইরে ধানের খেত–সবুজ সতেজ। অঘ্রানে বাতাসে ঢেউ লাগে ওদের বুকে। আমরা চেয়ে থাকি অপলক। কী জাদু আর কী মায়া আছে ওই ঢেউ-খেলানো সবুজ খেতে ইচ্ছে হয় সর্বাঙ্গ ভাসিয়ে কেবল সাঁতার কাটি ওই মনভোলানো শ্যামসায়রে। অশ্বথগাছের শোভাই কি কম? ওর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পাতা সদাই মুখর, সদাই চঞ্চল প্রাণহিল্লোলে। চৈত্রে কিছুদিন ধরে পাতা ঝেড়ে ফেলে রোদের কিরণ আর হাওয়া টেনে নেয় ও সর্বদেহে। তারপরে আসে একটা চেতনা। একটু সবুজের ছোপ লাগে ডালপালায়। তারপরে ঈষৎ লোহিত। ক্রমে সবুজ রং বদলায় দিনে দিনে–গাঢ় থেকে গাঢ়তর সবুজে।
সরকারি রাস্তাটার একধারে গ্রামের উচ্চ ইংরেজি স্কুল–আর একদিকে বন্দরের মতো হাটখোলা। ওখানে কামারশালে ঢং ঢং করে শব্দ হয় রাতের বেলা। ডগডগে লাল লোহার কণা ছিটকে পড়ে হাতুড়ির ঘায়ে। চমৎকার লাগে দেখতে ওই সৃষ্টিশালা–ওরা শুধু গড়ে।
গ্রামের রাস্তাঘাট গড়েছিল প্রতাপ রায় সদলবলে মাটি কেটে, মাথায় ঝুড়ি বয়ে। তার আগে চলার পথে কোথাও ছিল এক-হাঁটু জল, কোথাও একগলা। তারপরে কতই হল। কত প্রতিষ্ঠান–ইংরেজি বিদ্যালয়, বালিকা স্কুল, ঔষধালয়, দরিদ্র ভান্ডার, লাইব্রেরি আরও কত কী! এসবও সেই প্রতাপ রায়ের গড়া। ভোরে ঘুম ভাঙিয়ে দিত প্রতাপ রায়ের ঘণ্টা তারপরে উষাকীর্তন। শীতকালে খালে জল থাকত না ষষ্ঠী থেকে দশমী তিথি পর্যন্ত। সদলবলে প্রতাপ রায় টেনে বার করে দিত বিপন্ন মাঝিদের নৌকোগুলো। একবার এই শুকনো খালে আটকে পড়া নৌকোয় ধুকছিল দুটি জ্বরবিকারের রোগী। না ছিল ওষুধ, না পথ্য। তাদের কাঁধে করে ধরে নিয়ে যাওয়া হল আমাদের কাছারি বাড়িতে। সেবা হল দিনরাত। একটি বেঁচে গেল, আর রজনীকে পোড়ানো হল ওই সরকারি রাস্তার ধারে। গ্রামে ওষুধ-পত্তরের অভাব। প্রতাপ রায়ের চেষ্টায় যৌথ তহবিলে হল ঔষধালয়। অশ্বিনীকুমারের আদর্শ রূপায়িত করেছিলেন প্রতাপ রায়–অক্লান্ত শ্রমে। তাই তো তিনি আশীর্বাদ জানাতে আসতেন প্রতি উৎসবে। খুঁজলে আজও পাওয়া যাবে তাঁর পদরেণু।
রামচন্দ্র দাস ছিলেন প্রেমিক, কবি! ফর্সা রং–স্থূলহ্রস্ব দেহ। দুটি বড়ো বড়ো চোখ– প্রীতিরসে ঢলঢল। শুধু ভালোবেসে মানুষ গড়া যায়, তার উদাহরণ জোগালেন রামচন্দ্রবাবু। তাঁর দেহে-প্রাণে-মনে জ্যোতির ঝলক নামত ঊধ্ব থেকে অন্তরের গবাক্ষপথে। তাঁর প্রেরণা আসত যুক্তির পথে নয়, হৃদয়ের অজানিত অন্তঃপুর থেকে–শাশ্বত সত্যের চিরভাস্বর জ্যোতির মতো।
আজ প্রতাপ আর রামচন্দ্রের চিতাভস্ম মিশে আছে ওই পল্লির পথের ধুলোয়। যাঁদের কাছে এই ধুলো ছিল স্বর্ণরেণু তাঁরা ছিটকে পড়েছেন কোন দূর-দূরান্তে। কোথায় সেই নরেন্দ্রনাথ, অমৃতলাল, হরেন গুপ্ত আর রমেশচন্দ্র? তাঁদের চোখে হয়তো ধরণীর আলো হয়ে এসেছে নিষ্প্রভ।
কোথায় চলে গেল সেই অনন্তকুমার! যখন কালবৈশাখীর ঝড় উঠত-বাঁশঝাড়-গুলো ঝড়ের দোলায় নুয়ে পড়ত মাটির বুকে, তখন অনন্তকুমার আমাকে নিয়ে উঠতেন ওই উঁচু গাছের মগডালে। দেখতাম এলোকেশীর উন্মাদিনী মূর্তি। জীবনে যখন যা খাঁটি বুঝত তাই করত প্রাণ দিয়ে, জীবনের মূল সুরটি ছিল ভক্তির। সন্ধান করত তার–যে আড়ালে থাকে–ইশারায় ডাকে। লিখত সে চমৎকার, গানও গাইত অতিমধুর।
মনে পড়ে রসরঞ্জনকে। কুষ্ঠরোগীর সেবক নেই। পয়সা পাবে কোথায়-অনাহারে অনিদ্রায় পায়ে চলে নদী সাঁতরে শত শত মাইল চলল সে বৈদ্যনাথে রোগীসেবায়! এঁরা আজ কেউ নেই– কিন্তু আজও আছে ওই সুরেন। বেঁচে আছে সে আপন প্রভায়। শৈশবে ছিল সে কবি–ছবিও আঁকত চমৎকার। গৌরবর্ণ, মুখের কাঠামো মঙ্গোলিয়ান–দীর্ঘদেহ। জলের মোটা মোটা লম্বা জোঁকগুলো দেখলে আমাদের গা শিরশির করত। সুরেন ওগুলো ধরে এনে ট্যাঁকে করে ঘুরে বেড়াত–আমাদের ভয় দেখাত। সাপের ল্যাজ ধরে শূন্যে তুলে ও মজা দেখত! কল্পনা করত, কবিতা লিখত ভারত উদ্ধারের। ভারত উদ্ধারের কথা আমাদের মনে দাগ কাটত বেশি। দুর্জয়কে জয় করার আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠত আমাদের মনে। আমরা তখন কিশোর। দেহের পুষ্টির সঙ্গে এই বয়সে নেমে আসে শক্তিধারা–সে শক্তিকে অচঞ্চলভাবে ধারণ করতে পারে–এত শক্তি কার আছে? বাঁশ কেটে লাঠি বানাই–তরোয়াল, বন্দুক ধনুর্বাণ। কখনো কি মনে হয়েছে এই অস্ত্রে ইংরেজকে তাড়ানো যাবে না? তারপরে এল স্বদেশি আন্দোলন। আমাদের ভেতরে প্রেরণা জাগাল আনন্দমঠ, প্রেরণা জাগাল রামচন্দ্র দাসের কবিতা, মুকুন্দ দাসের সেই প্রাণমাতানো গান,
দশ হাজার প্রাণ যদি আমি পেতাম,
মাথায় পাগড়ি বেঁধে সাধক সেজে
দেশোদ্ধারে লেগে যেতাম।
আজ সেই দেশোদ্ধারী সুরেন, কবি সুরেন, চিত্রশিল্পী সুরেন পোশাক বদলেছে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোধা ডক্টর সেন এখন অবসরপ্রাপ্ত। যখন কৈশোরে বয়সের অনুপযোগী ইতিহাসের মোটা মোটা বইগুলো রাত জেগে পড়ত তখন একটি লোক তাকে উসকে দিতেন–তিনি আমাদের বরিশালের অশ্বিনী দত্ত। মনে আছে একবার সুরেন অশ্বিনীবাবুকে কবিতায় চিঠি দিল,
যাট বছরের বুড়ো তারে সবাই কেন বলে,
বুড়ো হয়ে যায় না শুধুই বয়স বেশি হলে।
সাদা হাসি আছে তাঁহার সাদা গোঁফের তলে,
বিশ বছরের যুবার মতো বুক ফুলিয়ে চলে।
আমি যদি মেয়ে হতাম, হতাম স্বয়ংবরা,
ওই বুড়োর গলে দিতাম তবে আমার মালাছড়া।
অশ্বিনীকুমারও জবাব দিয়েছিলেন তেমনি রসালো কবিতায়, সে-কবিতা আজ আর মনে নেই। ডক্টর সুরেন, ভাইস-চ্যান্সেলার সুরেন আজও তেমনি কিশোর, কিন্তু আপন জন্মভূমিতে সে অনাদৃত।
আমাদের এই খেলাঘরে জুটল এসে মনোরঞ্জন গুপ্ত! ভিন গাঁয়ের তরুণ। আজ বয়স তার যাট পেরিয়েছে, কিন্তু আজও সে কিশোর–গাছের পাতাটি ছিঁড়ে নিতে ওর দুঃখ হত, কিন্তু যখন ডাক এল গেরিলা বিপ্লবের, তখন এই বাঁধনছেঁড়া সাধকের হৃদয়-যন্ত্রে বাজল শুধু একটি তারের একতারা। দেশের মুক্তিযজ্ঞে হৃৎপিন্ড ছিঁড়ে আহুতি দিল নিজের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ। সরকারের খাতায় ওর মাথায় মূল্য বেড়ে যায়, কিন্তু আইনকানুনে ওকে ধরা যায় না–রাজসাক্ষী দেয় না ওর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য। তবু ওকে শিকল পরতে হল। নিজের পায়ে শিকল না পরলে কি মায়ের পায়ের শৃঙ্খল খোলা যায়? কিন্তু সে-শৃঙ্খল ‘চরণ-বন্দনা করে, করে নমস্কার। আজ দেশ তো বিদেশির গ্রাস থেকে মুক্ত হয়েছে, কিন্তু মুক্ত হয়নি ভয়, মুক্ত হয়নি মানুষের মন। দেবতাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে মানুষ। এই দুর্যোগে কে দেখাবে আলো? তাই নিরন্ধ্র অন্ধকার পথে একক অভিযাত্রী ওই ষাট বছরের কিশোর। প্রতিকারের হাত নেই, আছে দরদ, আজ অস্ত্র তো অবান্তর, তাই চোখে আছে জল-’সাত সাগরের জল। এই গ্রাম মনোরঞ্জনের খেলাঘর। আজ আর খেলার মাঠে সাথিদের কোলাহল নেই, কুটিরে কুটিরে জ্বলে না দীপ। নেই বালকদের পাঠাভ্যাসের উচ্চরব। সন্ধ্যায় ঠাকুরঘরে আর শঙ্খ বাজে না, আর কেউ জোটে না নৈশ রাতে খোল-করতাল নিয়ে কীর্তনে। তবু যেন শুনি। সেই গান,
মন রে তোর পায়ে ধরি রে,
একবার আমায় নিয়ে–একবার আমায় নিয়ে–
ব্রজে চলো–দিন গেলো, দিন গেলো!
কীর্তনের কথায় মনে পড়ে প্রিয়নাথের কথা–তার ছেলে মন্মথের কথা। আজ দু-জনের কেউ বেঁচে নেই।
কী চমৎকার ওরা গাইত! প্রিয়নাথের ডাকনাম ছিল মুলাই। দু-দলে পাল্লা দিয়ে গান চলেছে। দোহার বালকদের সংযত করে মুলাই ট্যারা চোখ ঢেলা ঢেলা করে গান ধরে,
হল দেহ-তরি ডুবু ডুবু প্রায়
পড়ে অকূলে আজ অসময়
***
তরির নব ছিদ্রে বহিছে বারি-ই-ই,
তাহে পাপের বোঝা নয় রে সোজা
উপায় কী করি।
এখন একূল ওকূল দু-কূল যায়–
শেষটা বলে যখন হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে ঘুরে ঘুরে সে গাইত-শ্রোতারা হরিধ্বনি দিয়ে উঠত তখন। মুলাইর ডাগর চোখ ভিজে উঠত জলে। পাশের গ্রাম যশুরকাটির ভজরাম সেন বড়ো গায়ক। সে ছিল ওর শ্বশুর। প্রায়ই গান হত তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। শ্বশুর বলে সে রেহাই পেত না। মুলাই বলত দোহারসহ,
শোন রে ভজা শোন,
আর আর পক্ষে যেমন তেমন
তোমার পক্ষে যম।
ভজরামও জবাব দিত যোগ্য ছন্দে।
ওদের গান আজও কানে বাজে। ভুলতে পারি না গোপাল ভদ্রের সেই আকুতি,
ব্রজের পথে হায় রে নিতাই,
যদি মোর দেহ পতন হয়–
তবে কৃষ্ণ-নাম লিখো আমার গায়–
ওই তুলসী মৃত্তিকাতে কৃষ্ণ-নাম লিখো–-আমার গায়।
মনসার ভাসান রয়ানি গান হত একাদিক্রমে সাতদিন ধরে। বেহুলার দুঃখের অন্ত নেই কলার মাজুসে স্বামীর অস্থি নিয়ে গাঙের জলে ভেসে চলে বেহুলা সুন্দরী। সেই নদীতীরে গোদা বঁড়শিতে মাছ ধরে।
বুড়িয়া গোদা বঁড়শি বায় তলা বাঁশের ছিপ,
সুন্দরীরে দেইখ্যা গোদা ঘন মারে টিপ।
পেছনে সমবেত কণ্ঠে দোহাররা ধুয়া গায়, ‘বড়ো তা-আ-আপিত’।
ভিন দেশ থেকে আসত কালা বৈরাগী রামায়ণ গাইতে। বাঁকা ঠোঁট বাঁকা চোখ–গলাটা ছিল মিঠে আর ধারালো। সেই গানের কথা আজও দুঃখের দিনে সান্ত্বনা দেয়,
রাম নামের গুণে জলে ভাসে শিলে–এ-এ।
এদের কেউ আর বেঁচে নেই–ওদের গানের রেশ আজও বাজে ওই অশ্বথের পাতায় আর বাঁশবনের মর্মর শব্দে।
গ্রাম্য কবি হারাধন ছিল খোঁড়া। লাঠি হাতে একখানা পা একপাক ঘুরিয়ে স্থির হলে তবে চলত অন্য পা-খানা। কবি বাণীকণ্ঠও ছিল ট্যারা–রচনা ছিল গ্রামের ভাষায়। তারাও নেই, আর তাদের রসিক শ্রোতারাও পালিয়ে গেছে তেপান্তরের মাঠে। গ্রামের যুবকদের মধ্যে কত শত হয়েছে গ্র্যাজুয়েট, কত অধ্যাপক; পি. আর. এস. হয়েছে চারজনা, ক-জনা পি-এইচ. ডি; বিলেত থেকেও ডিগ্রি এনেছে কত সোনার ছেলে, কিন্তু পল্লিমায়ের অদৃষ্টে নেই তাদের মিলিত সেবা পাওয়া! কে. ভি. সেন এনেছিল হাফটোন ব্লকে যুগান্তর; জ্যোতি গড়েছিল আর্টস্কুল। তাঁদের শিষ্য-উপশিষ্যেরা ছড়িয়ে আছে ভারতময়। প্রত্যেক ব্লকের কারখানায় তারাই কর্ণধার। বিলেতে পাস দিয়ে অশ্বিনী সেন গড়লেন হুগলি কটন মিল, দেশের শিল্পে সুর দিলেন গোপাল সেন, দর্শনশাস্ত্রে রস জোগালেন নিবারণ দাশ, দেশবন্ধুর ভগিনী বিয়ে করলেন অনন্ত সেনকে তাঁর কৃতিত্বের আকর্ষণে। তাঁদের অর্থে সম্ভব হল দেশের শিক্ষাদীক্ষা। তারাপ্রসন্ন ব্যয় করলেন মুক্ত হাতে, কিন্তু আজ তাঁদের ঘরে আর দীপ জ্বলে না! রাস্তাঘাট আগাছায় আচ্ছন্ন!
তবু ভুলতে পারি না সেই পল্লিমাকে। বৈশাখে মেলা বসত বটতলায়, আর অশ্বতলায়। দেশি কাঠের পুতুল গড়ে আনত শিল্পী অধরচাঁদ। আর আসত মাটির পুতুল হাঁড়ি-কুড়ি। ফুটি তরমুজও মেলায় আসত রাশি রাশি। সন্ধ্যায় ঠাকুরঘরে ওই ফুটি, তরমুজ, ডাব, ফেনি বাতাসা, চিনির খেলনায় দেওয়া হত নারায়ণের ‘শীতল’। কী মজা ছিল প্রসাদ পেতে! ঘরে ঘরে জমা থাকত মুড়ি, চিঁড়ে, কলা, নারকেল, পাটালি। গাছে গাছে পাওয়া যেত আম, জাম, কাঁঠাল, গাব, ডউয়া, কামরাঙা, লিচু, জামরুল, আরও কত ফলমূল।
শ্রাবণে মনসা পুজো, ভাদ্রে বিশ্বকর্মা পুজোর বাচ, আশ্বিনে দশহরা। ভাদ্রসংক্রান্তি আর দশহরায় আসত লম্বা লম্বা ছিপ-নৌকা। সারি সারি জোয়ান বসত দু-ধারে। বাবরি দুলিয়ে মাঝি ধরত হালের বইঠা। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা ছিল না এতটুকু। উৎসবে-পুজো-পার্বণে– ওরাই কর্মী, ওরাই লেঠেল–বাচ খেলে ওরাই। আমরা খালের কিনারে নৌকায় বসে বাচ দেখতাম। খালের জলে ঢেউ উঠত কূল ছাপিয়ে-দুলিয়ে দিত আমাদের নাও।
কার্তিকে রাসপূর্ণিমায় মেলা বসত বাটাজোড়ে। বাটাজোড় মেলার পরেই অঘ্রান মাসের নবান্ন। সোনার ধানে ভরে যেত গৃহস্থের আঙিনা। নবান্নে সবাইকে নেমন্তন্ন জানাতে হবে। মানুষ, পশুপাখিকেও ডাকতে হবে। মনে পড়ে বড়ো বড়ো গাছের কাছে গিয়ে উচ্চস্বরে বলতাম,
ও দাঁড়কাক, ও পাতিকাক
আমাদের বাড়ি শুভ-নবান্ন
তোমরা সবাই যাইয়ো,
চাল, কলা, গুড়, সন্দেশ
পেটটি ভরে খাইয়ো।
মনে পড়ে দেশপূজ্য অশ্বিনীকুমারের একখানা পুরোনো চিঠি পড়েছিলাম অনেকদিন আগে। চিঠিখানা লিখেছিলেন তিনি তাঁর স্ত্রীকে পাঞ্জাব থেকে প্রায় বছর সত্তর পূর্বে। গুরুগোবিন্দ, রণজিৎ সিং, দিলীপ সিং প্রভৃতির কীর্তিকলাপ, তাঁদের অস্ত্রাগার, সমাধিস্থল প্রভৃতি দেখে তাঁর মনে একাধারে যে আনন্দ ও বেদনার উদ্রেক হয়েছিল তাই প্রকাশ করেছিলেন তিনি ওই পত্রে। দীর্ঘ পত্রের একস্থানে তিনি লিখেছিলেন,
…ভারতলক্ষ্মী অবশেষে এই বিশাল ভারতভূমির উত্তর-পশ্চিমে পাঞ্জাবে আশ্রয় লইয়াছিলেন, আজ সেই স্থান হইতেও দূরীভূত হইলেন। ওই অস্ত্রাগারের সম্মুখে বসিয়া শুধু মনে হয় যদি সমস্ত ভারতবাসী পরস্পরের গলা ধরিয়া দুঃখের কাহিনি গাহিয়া ক্রন্দনের রোল তুলিয়া কাঁদিতে পারিত তবে বুঝি কষ্টের কিঞ্চিৎ উপশম হইত। কিন্তু তাতেও বাধা, ‘ফুটিয়া ফুকারি কাঁদিতে না পাই’ এমনি আমাদের দূরদৃষ্ট।…একবার মনে হয় গুরুগোবিন্দের ঢালখানি নিয়া পলায়ন করি, মনে হয় ওই পতাকাগুলি, অস্ত্রগুলি কলঙ্কের নিদর্শনস্বরূপ রাভি নদীজলে বিসর্জন দেই; মনে হয় দলীপের ক্রীড়াসামগ্রী কামানটি বুকে করিয়া উচ্চতরালে কাঁদিতে থাকি–কত কী ভাব হয় কী লিখিব?
দেশনায়ক অশ্বিনীকুমার দেশের অতীত গৌরবের অবমাননা দেখে কেমন মর্মাহত হয়েছিলেন, এ চিঠি থেকেই তা বোঝা যাবে। তাঁর প্রিয় বাংলা, তাঁর প্রিয় বরিশালের আজকের রূপ যদি তাঁকে দেখতে হত কী করে তিনি তা সহ্য করতেন?
.
চাঁদসী
গ্রাম নয়। জননী। আমার পিতৃপুরুষের জন্মভূমি। তাঁদের জীবনপ্রভাতে শঙ্খধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছিল এ গ্রামের বাতাস, জীবন-সূর্যাস্তে তাঁদের চিতাবহ্নি নিবিয়েছে এ গ্রামের জলরাশি। এ গ্রামেই প্রথম সূর্যালোকের সঙ্গে আমার পরিচয়। আজ সে গ্রাম থেকে চলে এসেছি অনেক দূরে, তবু সেই নবান্নের ঋতু, পুজোর ঋতু, আকাশডাকা ঋতু আমার সমস্ত অস্তিত্বকে আচ্ছন্ন করে দেয়। আমার চিন্তাধারার স্তরে স্তরে লেগে আছে সেই গ্রামটির প্রতি অসীম মমত্ববোধ। সে-গ্রামের পরিচয় লিখতে গিয়ে আজ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে আসছে দুটি চোখ। সে-গ্রামকে যে কিছুতেই ভুলতে পারছি না। দুঃখদৈন্য নিরাশাম্লান শরণার্থী জীবনে আমার জননী, আমার ছেড়ে-আসা গ্রামের স্মৃতি এখন আশার প্রদীপশিখার মতো অনাহত ও অমলিন।
কলকাতায়, শুধু কলকাতায় কেন, বাংলাদেশের সর্বত্রই চাঁদসীর ক্ষত চিকিৎসকরা খ্যাতি অর্জন করেছেন। এই চাঁদসী পূর্ব বাংলার বরিশাল জেলার একটি গ্রাম, সে-গ্রামই আমার জন্মভূমি। দেশ-বদলের পালায় সে-গ্রামকে ছেড়ে এসেছি, কিন্তু শত দুঃখের দিনেও চাঁদসীর মানুষ বলে নিজে গর্ব অনুভব করি, দেশের কথা মনে হলে কেমন একটা প্রশান্তিতে ভরে যায় এই হতাশার মুহূর্তগুলো। গ্রাম তো শুধু আমার একার নয়, হাজার মানুষের গ্রাম চাঁদসী। শুধু আজকের নয়, কতকাল ধরে কত মানুষের পদচিহ্নে এ গ্রাম ধন্য। সে-ইতিহাস আজ হয়তো সকলের মনে নেই, কিন্তু সে-গ্রাম আজও রয়েছে অতীতের নীরব সাক্ষ্যের বাণী বহন করে। গ্রামের কথা লিখতে বসে সে ইতিহাসের পূর্ণ পরিচয় দেবার সামর্থ্য আমার নেই, কিন্তু আমার নিজের সঙ্গে গ্রামের যে মধুর পরিচয়টুকু জড়িয়ে আছে সে-কাহিনিই আজ জানিয়ে যাই।
অনেকদিন ছেড়ে এসেছি গ্রামকে। কিন্তু সেখানকার প্রতিটি দিনের কাহিনি আজও আমার সারামন জুড়ে রয়েছে। গরমের ছুটিতে কলেজ ছুটি হলেই গ্রামে যাওয়ার জন্যে মন ব্যাকুল হয়ে উঠত। জলের দেশ বরিশাল। স্টিমার কতক্ষণে গিয়ে পৌঁছোবে গৌরনদী স্টেশনে, সেজন্যে কী ব্যাকুলতা। ঘাটে পৌঁছেলেই সোনামদ্দি মাঝি চিরপরিচিত হাসি হেসে প্রশ্ন করত—‘কর্তা, আইলেন নাকি, চলেন, নৌকা আনছি। আপনারা যে আজি আইবেন হেই তো আমি জানতামই। আমিও আপনাগো মতো দিন গুনি কবে আপনেরা আইবেন। তা কর্তা, গায়-গতরে ভালো আছেন তো?’
এইরকম কতশত প্রশ্ন করত সোনামাঝি। সে বুঝত বাড়ি পৌঁছোবার জন্যে আমাদের আগ্রহ। তাই খুব তাড়াতাড়িই নৌকো চালাত সে, বলত, ‘ওই যে কর্তা লোহার পোল দেহা যায়।’ এই পুলটি ছিল আমাদের বিশ্রামের জায়গা। সেখানে বর্ষার দিনে দেশ-দেশান্তরের নৌকা এসে ভিড়ত পণ্য বহন করে। আর একটু এগোলেই কাঁপালীবাড়ি, আমাদের গ্রামে ঢুকবার দক্ষিণ প্রান্তের প্রবেশমুখ। আর একটু এগিয়ে যান, দেখতে পাবেন একটি কাঠের পুল, তার পাশেই ঝাঁকড়ামাথা একটা আমগাছ। খবরদার, রাত্রিবেলা অন্ধকারে সেদিকে যাবেন না। গেলেই হয়তো গাছের ডাল থেকে ঝুলে-পড়া কোনো নারীমূর্তি দেখে আপনি চমকে উঠবেন। স্বামীর অত্যাচারে এক বাজনদারের বউ ওই গাছটায় গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে আত্মহত্যা করেছিল। খুব ভয় করত বই কী সে-গাছের তলা দিয়ে যেতে। এমনি ভয় করত কালীবাড়ি ও জয়দুর্গা খোলা দিয়ে যাবার সময়ও। যাই হোক, ঝাঁকড়া আমগাছটা পেরিয়ে বাজনদার বাড়ি ছাড়িয়ে গেলেই চোখে পড়বে বিখ্যাত দিঘির ঘাট। এই দিঘির ঘাটটা ছিল আমাদের লেক। গ্রীষ্মের কত সন্ধের মধুর স্মৃতি জড়িয়ে আছে সেই দিঘির পাড়ে, কাকচক্ষুর মতো স্বচ্ছ জল। তার কিছুটা দূরেই গ্রামের ডাকঘর। সেখানে প্রতিদিন সকালবেলা গ্রামের লোক সব জড়ো হত। চলত আলাপ-আলোচনা, চলত খবরের কাগজ পড়া। ওরই দক্ষিণে গুহদের বাড়ি। কত জাঁকজমক ছিল ওবাড়ির, গমগম করত দিনরাত। পুজোর সময় গ্রামের সকলেই এসে জমত এবাড়িতে। তার দক্ষিণে মজুমদার বাড়ি; আরও এগিয়ে যান। কালীবাড়ি, দশমহাবিদ্যা বাড়ি, কেদারবাবুর বাড়ি হয়ে চলে আসুন তালুকদার বাড়ি, গ্রামের একেবারে শেষসীমান্তে। পায়ের জুতো খুলে দেখুন একুটও কাদা লাগবে না, বর্ষাকালেও না। এত সুন্দর ও চমৎকার এ গ্রামের পথঘাট।
গ্রামটি ছোটো হলেও এখানে চার-চারটি থিয়েটার পার্টি ছিল। বিষহরি নাট্য সমিতি, দশমহাবিদ্যা নাট্য সমিতি, সিদ্ধেশ্বরী নাট্য সমিতি ও চাঁদসী আর্ট প্রোডিউসার্স–সংক্ষেপে সি. এ. পি.! এই শেষোক্ত পার্টিই ছিল গ্রামের মধ্যে সেরা। এদের দলেই গ্রামের শিক্ষিত যুবকবৃন্দ অংশগ্রহণ করত। পুজোর সময় থিয়েটার নিয়ে কী মাতামাতিই না হত! কত দলাদলি, ঘোঁট পাকানো, জব্দ করার ফন্দি, এসব মত্ততার মধ্য দিয়েই পুজোর কটা দিন কেটে যেত। পুজোয় দেশে যাওয়ার আনন্দই ছিল ওর মধ্যে। এই থিয়েটারে অভিনয়ে যাঁরা অংশগ্রহণ করেতেন তাঁদের মধ্যে দুই সহোদরের কথাই বিশেষ করে মনে পড়ে, হবিবর রহমান ও লুৎফর রহমান ওরফে বাদশা মিঞা। বাদশা মিঞা আজ পরলোকগত। এমন সুন্দর চেহারা, শিক্ষিত ও অমায়িক লোক খুব কমই দেখেছি। এরা দুজনে সমস্ত অভিনয়েই অংশগ্রহণ করতেন এবং তাও প্রায়ই হিন্দু-দেবতার ভূমিকায়! আজ একথা শুনলে ইসলাম ভক্তরা চোখ কপালে তুলবেন জানি, কিন্তু সেদিন এ ছিল সত্য, স্বপ্ন নয়। মধু শেখ গ্রামের সকলেরই কাছে ছিল অতিপরিচিত, আপন বন্ধুজন। তার একটি বিশেষ গুণ ছিল। সে সমস্ত পশুপাখির ডাক নকল করতে পারত আর তা শোনাবার জন্যে গ্রামের সমস্ত মেয়েমহলেও তার ডাক পড়ত। সেও আজ পরলোকগত। কত লোকের কথাই তো আজ মনে এসে ভিড় করছে কার কথা লিখব, রজনী গুহমশায়ের বাড়ির কথা কী ভোলা যায়, না ভোলা যায় তাঁর বাড়ির সকলের অমায়িক ব্যবহারের কথা? এই বাড়িতেই চলত থিয়েটারের মহড়া দিনরাত। চলত গান-বাজনা। কারণ গান-বাজনার সমজদার ছিলেন এ বাড়ির সকলেই, আর সকলেই ছিলেন সুকণ্ঠ। নিম্নশ্রেণির মধ্যে আরও অনেকের গান আমাদের মুগ্ধ করত। দিনের কর্মাবসানে এরা একত্রে মিলিত হত। রাত্রিতে অনেকের বাড়িতে ‘ত্রিনাথ’-এর মেলা বসত। খোল, করতাল, মৃদঙ্গ সহযোগে চলত ঠাকুর ত্রিনাথের ভজন। কী সুন্দর তার মূৰ্ছনা! কোনো এক আত্মভোলাকে দেখেছি জ্যোৎস্না রাতে নির্জন স্থানে বসে একটি একতারা সহযোগে অপূর্ব সুরজাল সৃষ্টি করে বাউল সংগীত গেয়ে চলেছে। সে-সংগীত শুনে ঘর ছেড়ে তার পাশটিতে এসে চুপ করে বসে থাকতে হত। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ত শ্রোতা ও গায়ক উভয়েরই। সংগীত শেষ হলে মনে হত কোন স্বর্গলোক ভ্রমণ করে এলাম এতক্ষণ। সেই আত্মভোলা আর তার সংগীত কি আজও বেঁচে আছে!
সেবারের শীতকালের একটি মজার ব্যাপার বলবার লোভ সামলাতে পারছি না। ডিসেম্বরের কনকনে শীত; সকলে মিলে বকুলতলার খালে মাছ ধরা হচ্ছে, এই মাছ ধরা ছিল আমাদের বড়দিনের উৎসবের একটি অঙ্গ। হঠাৎ খবর এল গ্রামে বাঘ এসেছে। দল বেঁধে চললাম সেই অকুস্থলে। চাক্ষুষ দেখার পর স্থির করলাম, তিনি একটি ক্ষুদ্র সংস্করণের নেকড়ে ছাড়া আর কিছুই নন। কিন্তু সেই ক্ষুদে নেকড়েই আমাদের গ্রামে যে নাটক অভিনয় করে গেলেন তার মধ্যে করুণ ও হাস্যরস দুই-ই ছিল, আঠারোটি লোক ঘায়েল হয়েছিল তার সঙ্গে লড়াইয়ে। মরতে মরতে বেঁচে গেছে তারা। এটাই ছিল করুণরস। হাস্যরসের কথা উল্লেখ করতে সত্যি আজ হাসি পায়। চার-পাঁচজন বীরপুঙ্গব যারা তাদের পাকা শিকারি বলে গ্রামে জাহির করত, তারা তাদের সম্মিলিত চেষ্টা দ্বারাও শেরের বাচ্চার কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারেনি, যতবারই তারা দু-তিনজন একসঙ্গে গুলি চালিয়েছে বাঘের গায়ে, ততবারই দেখা গেছে ব্যাঘ্রমশায় তার লাঙুলটি নাড়তে নাড়তে বহাল তবিয়তে অন্য ঝোপে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। সারাদিন ধরে সংঘবদ্ধভাবে আক্রমণ করা হল কিন্তু সবই ব্যর্থ, সবই বৃথা। শেষদিকে কয়জন শিকারি বাঘের হাতে সাংঘাতিকরকম জখম হয়ে বাঘ মারার বাহাদুরি নেওয়ার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে হাসপাতালে আশ্রয় গ্রহণ করল! আর সন্ধের অন্ধকারে ব্যাঘ্র মামাও তার এ গ্রামের লীলা সাঙ্গ করে বহাল তবিয়তে অন্য গ্রামে গিয়ে লীলাখেলা আরম্ভ করলেন!
এমনি কত ঘটনা আজ মনে পড়ছে। ‘নীল খেলার মাঠে’ ফুটবল খেলা, সন্ধের অন্ধকারে ‘ধরের ভিটা’য় দল বেঁধে ডাব চুরি করতে যাওয়া, আরও কত কী! বেচারাম ধুপী চৌকিদারি করত, শাসাত। কিন্তু ডাব নিয়ে যেতে বাধা দিত না বড়ো একটা। শৈশবের এসব কাহিনি ভুলতে পারি না। মনে পড়ছে গ্রীষ্মের দুপুরে বটগাছের ডালে বসে টোটাল পাখি একটানা সুরে টুপ টুপ করে গেয়ে যাচ্ছে। ঘুঘু-ডাকা অলস দুপুর। গ্রামের ছায়া-সুনিবিড় এক-একটা বাড়ি। তেমনি নীরব নিরালা বাড়িতে বসে সে-ডাক শুনতে কী ভালোই না লাগত! আজ সেসব হারিয়ে শহরে এসে মাথা গুঁজবার ঠাঁই খুঁজছি, তাও মেলে না। এই অনাদৃতদের আবার ঘরে ডেকে নেবে কে? অসহ্য বেদনায় আজ কেবল কবি বিহারীলালের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে,
সর্বদাই হুহু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন,
চারিদিকে ঝালাফালা
উঃ কী জ্বলন্ত জ্বালা!
অগ্নিকুন্ডে পতঙ্গ পতন।
এ অগ্নিকুন্ড থেকে আমাদের কি উদ্ধার নেই? পতঙ্গের মতোই কি আমরা শুধু আত্মাহুতি দিয়ে যাব? কিন্তু কোন মহত্তর কল্যাণের জন্যে এই মৃত্যুযজ্ঞ? সমগ্র দেশের ভিত যে কেঁপে উঠছে এ বীভৎসতায়!
.
সৈওর
সুগন্ধা নদী। সুদর্শন চক্রে গৌরীর খন্ডিত নাকটি এই নদীগর্ভে পড়েছিল। ভোর হয়ে আসে। দাঁড়কাকের টানা-টানা থামা-থামা ব্যথা-গম্ভীর ডাক, কোকিলের অশান্ত কাকলি। আকাশছোঁয়া টেলিগ্রাফের তার। বাঁ-দিকে ‘সুতালরি’র মাথা ভাঙা মঠ। সুতালরির পোশাকি নাম ‘সূত্রলহরি’। মাথা ভাঙা কেন? কোন সন্তান মায়ের চিতায় এই মঠ তোলা শেষ হলে বলেছিল, শোধ করলাম মাতৃঋণ, অমনি ভেঙে পড়ল মঠের মাথা। সত্যিই তো, মাতৃঋণ কী কেউ কখনো শোধ করতে পারে?
আমাদের গ্রামটি যেন স্বয়ংসম্পূর্ণ। সেখান থেকে কখনো কেউ বিলেত যায়নি, সে-গ্রামে কোনো কোঠাবাড়ি নেই, এম. বি. ডাক্তার নেই, কোনো বাড়িতে চাকর পর্যন্ত নেই, কোনো ক্লাব নেই, লাইব্রেরি নেই, পলিটিক্যাল পার্টি নেই। এমন একটি গ্রামের কথা বলতে বসেছি, যে গ্রামের লোকদের মন আজও শহর থেকে অনেক অনেক দূরে।
সামনেই নলচিটি। ছবির মতো ছোট্ট পন্টুনখানা। নদী এখানে আরও চওড়া। পাড়ে পাড়ে স্টিমারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে, আলো-নেভা লণ্ঠন, সড়কি-বলয় আর চিঠির ঝোলা কাঁধে ‘রাণার ছুটেছে, রাণার’। স্টেশনের ওপারে ষাটপাইকা গ্রাম। ওখানে নাকি একদা ষাটজন বিখ্যাত পাইকের বাস ছিল।
এখানে নেমেই ধরতে হয় আমাদের গ্রামের পথ। কিছুটা পথ হেঁটে অথবা বর্ষাকালে নৌকায় যেতে হয়। অন্য সময় খালগুলো কচুরিপানায় ঠাসা থাকে। যারা গ্রামে যায়নি, ফুটে থাকা কচুরি ফুলের খবর তারা জানে না। পার্ক স্ট্রিট রিফিউজি ক্যাম্পে থাকার সময়, সাহেবদের বাড়ি সাজানোর জন্যে মাঝে মাঝে কয়েকটি করে কচুরি ফুল বিক্রি হতে দেখতাম।
নৌকা গ্রামের খালে এলেই, দু-দিকের সারি সারি ধানের খেতে খেতে, দূরের আম সুপুরি-তাল-নারকেল গাছগুলোর ডগায় ডগায়, উড়ে যাওয়া কাকের বকের পাখায় পাখায়, দূর-দূরান্তব্যাপী নীল আকাশে, এককথায় পথের সর্বত্র যেন পেতাম কেমন একটা স্নেহস্পর্শ। সেখানে লজ্জা নেই, সংকোচ নেই, একেবারে খাঁটি উন্মুক্ততা। লগির খোঁচা খাওয়া নৌকায় তলাকার জলের মতোই মন তখন আনন্দে ছলছলিয়ে উঠতে থাকে।
হাঁটাপথে নলছিটির পর নরসিংহপুর, বৈচন্ডি, আখখারপাড়া, হয়বাৎপুর বা হবিৎপুর, তারপর আমাদের গ্রাম সৈওর। সৈওর গ্রামটি এদের মধ্যে সবচেয়ে ছোটো। স্টিমারের সঙ্গে যেমন গাদাবোট থাকে, হবিৎপুরের সঙ্গে সৈওর গ্রামটিও ঠিক তেমনি। আমাদের গ্রাম বলতে আমরা বুঝি হবিৎপুরকে, বলেও থাকি তাই। হাট, বাজার, পোস্ট অফিস, হাই স্কুল, খেলার মাঠ সবই হবিৎপুর ও আখোরপাড়ার। এখানে মুসলমানেরা সংখ্যায় অনেক। আমাদের ঢোলবাদক আর কুমোররা বরিশালের মধ্যে বিখ্যাত। জামাইবাবু, পিসেমশাই ও মামারা আমাদের গ্রামকে পান্ডব বর্জিত দেশ বলতেন। অফুরন্ত মাছধরা আর গোয়ালের গোরুগুলো না থাকলে তাঁরা নাকি আমাদের ওদিকে যেতেনই না। অবশ্য কলকাতার খবরের কাগজ শহরের আগেই আমরা পেতাম। নলছিটি বরিশালের আগের স্টেশন, মাত্র ছ-ক্রোশ পথ।
এককালে কোনো শক্ত জমিদার এই কয়েকখানি গ্রাম বসবাসের জন্যে নির্দিষ্ট করেছিলেন। তাই কয়েকটি খুব বড়ো বড়ো দিঘি দেখতে পাওয়া যায়। চন্ডীদাসের দিঘি সবচেয়ে বড়ো। তার চারদিকে এখন গা-ছম ছম-করা অরণ্য আর শীতল স্তব্ধতা। দূর কুটিরের টেকিপারের ঠুকঠুক শব্দ-লাগা প্রচন্ড দুপুর ঝিমুতে ঝিমুতে কেঁপে কেঁপে ওঠে। খেজুর ফুলের গন্ধভরা নিরিবিলি পায়েচলা পথ রোদে ঝাঁঝরা শেওলাখোলার পাশ দিয়ে চন্ডীদিঘির ছায়া মেখে কোথায় যেন চলে গেছে! এ দিঘির পারে বসে শ্রান্ত পথিক তার কো-কলকেটি বের করে নিয়ে বুটুর বুটুর তামাকটানা সুর শোনায়। তারপর রাজাবাড়ির দিঘি। এখানে বড়ো বড়ো মেঘডম্বুর সাপ অনেক মারা হয়েছে। দিঘিটি জমাট ঝোপে ঢাকা। তার ওপর গোরু চরে বেড়ায়। কিন্তু পৌষসংক্রান্তির দিন থেকে এক পক্ষকালের জন্যে সব ঝোঁপ তল পড়ে। এর বৈজ্ঞানিক কারণ কী তা জানা যায়নি। তবে ঘটনাটি অনেকবার দেখা। তৃতীয়টি সম্প্রতি আঁধি। চারধারে হোগলা, ভেতরে ফণাধরা সাপ আর জলপদ্ম। পাড় খুব উঁচু, সেখানে ছেলেদের খেলবার মাঠ। সুপুরির সময় এখানে চটি পড়ে। শ-খানেক গোল গোল চকচকে বঁটি, আঙুলে ন্যাকড়া জড়িয়ে লুকা জ্বালিয়ে চটির লোকরা কাজ করে আর গান গায়। এক-একটি বড়ো বড়ো চালান শেষ হবার অবসরে গান হত ‘গুণাবিবির পালা। রাত-মাতানো হইহই আর কী বেদনা সে-কণ্ঠে,
ও নাথ, গুপ্ত হন গুপ্ত হন
পুলিশ এসেছে,
আপনার চাচা ধলু মেয়া এজাহার দিছে।
আবার গেয়েছে,
ও–গুণা, গুণা গো,
আর কেন্দো না, কেন্দো না, দেশে চলে যাও,
নয়লাখ টাকার জমিদারি বেচে বেচে খাও।
গ্রামের ছেলে-মেয়েদের মুখে মুখে কিছুকাল পর্যন্ত এসব গানই চলতে থাকে। শোনা যায়, এককালে এ গ্রামের ভোজ উৎসবের সব বাসনপত্র এই দিঘির জলে ভেজানো পাওয়া যেত, ভোজশেষে তা আবার দিঘিকে ফিরিয়ে দিয়ে যাবার প্রথা ছিল। কিন্তু কোনো শাশুড়ির শ্রাদ্ধের নেমন্তন্নের পর কোনো বউ নাকি দু-একটি বাসন লুকিয়ে রেখেছিল, তারপর থেকে আর কেউ কিছু পায় না। এই জলে নাকি এক-একরকম মাছ দেখা যায়, তাদের মাথায় ধূপদানি, কপালে টকটকে লাল সিঁদুর।
কেউ কেউ বলে, এসব গ্রামে আগে নাকি গভীর অরণ্য ছিল, আর একদল ডাকাতই ছিল এখানকার আদিম বাসিন্দা। কথাটা হয়তো মিথ্যে নয়। কারণ সমস্ত গ্রামটিতে দুর্গা পূজা অপেক্ষা কালীপূজারই বেশি ধুম। প্রায় বাড়িতেই, আমাদের বাড়িতেও, প্রাচীন আমলের বড়ো বড়ো ঢাল সড়কি এখনও অনেকগুলোই আছে। ঠাকুরদাদা হাঁটু ভেঙে একহাতে বড়ো বড়ো মোষ বলি দিতেন। সুগভীর রাত্রিতে ঘড়ি-ঘণ্টায় ঘুম ভেঙে পুজোমন্ডপ থেকে ঠাকুরদাদার কালীপুজোর মন্ত্র উচ্চারণ শুনতাম। ওঁ হ্রীw প্রভৃতি এক-একটি শব্দের ঝংকারে ঘরের কড়িকাঠগুলো যেন ঝন ঝন করে কেঁপে উঠত। গ্রামের নর বা ঢোলবাদকরা একত্রে এক এক বাড়ি করে বাজনা বাজায় ও আলতি হয়। যারা শোলার ফুল তৈরি করে, তাদের বলে বনমালি। বনমালি সব বাড়ি বাড়ি আলতির সময়ে ভাঙের ব্যবস্থা নিয়ে আসে। সমস্ত গ্রামের লোক একত্রে এক-এক বাড়ির প্রতিমা বিসর্জন দেয়। পুজোয় কে কত বড়ো শিংওয়ালা ছাগ বলি দিল এ ব্যাপারটি ছাড়া আর সব ব্যাপারেই সারাগ্রামের অদ্ভুত একতা। কোনো বাড়ির নেমন্তন্নর ব্যাপারে প্রত্যেক বাড়ির পুকুর থেকেই নির্বিবাদে চলত মাছ ধরার উৎসব। কোনো বাড়ির জামাই এল তো এ যেন সারাগ্রামখানারই জামাই এল, তখন গ্রামসুদ্ধ প্রত্যেক বাড়িতেই একটা সুন্দর সুলজ্জ পরিচ্ছন্নতা দেখা যেত।
গ্রামের কালীবাড়িটি গভীর অরণ্যের মধ্যে। প্রতিবছর পুজোর পাঁচ-সাত দিন আগে থেকে জঙ্গলে আগুন লাগানো হত। নির্দিষ্ট দিনে পূর্ববছরের প্রতিমা ভাসান দেওয়ার বিধি। পুজো হয় পূর্ণিমার দিন। গাঁয়ের ‘তিন মাথা লোকেরা এই পুজোর দিন ঠিক করেন। শতাধিক বছর আগের কালীমন্দির! বট-অশ্বথের শেকড় জড়ানো তার আপাদমস্তক। কালের হাওয়ায় সর্বাঙ্গের ইটচুন গেছে খসে, তাই ইদানীং সেটি একটি সুদৃশ্য শেকড়ের মন্দির-গুহার রূপ ধারণ করেছে। তার মধ্যেই আবার বেল গাছ, জবাফুল গাছ, কচি দূর্বার ছড়াছড়ি।
গ্রাম্য ব্রাহ্মণ কায়স্থ শূদ্র সবাই গোঁড়া puritan, কিন্তু এই পুজোর দিনের প্রথা অনুসারে, বাল-বৃদ্ধ পন্ডিত-মূর্খ ব্রাহ্মণ-শূদ্র সবাই একত্রে গা ছুঁইয়ে প্রসাদ খেতে বসে। মাংস দিয়ে খিচুড়ি আর পায়েস। সেদিন গ্রামের কোনো বাড়িতেই রান্না হয় না। সবাই উবু হয়ে খেতে বসে। প্রথমবারের পরিবেশন হলেই ঘোষাল একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে হাঁক দিয়ে বলে–‘ও ভাই সাধু!’ সবাই তখন সমস্ত শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলে- ‘হেঁইও’, ঘোষাল বলে–’ডাইল খাইলা’, সবাই—’হেঁইও’, ঘোষাল—’তরকারি খাইলা’, সবাই—‘হেঁইও’, এইভাবে।
আরও খাইলা ভা–জি,
হেঁইও, হেঁইও, হেঁইও!
মহামায়ার,
হেঁইও!
পেরসাদ খাইয়া,
হেঁইও!
মন করিলা রাজি–
হেঁইও, হেঁইও, হেঁইও।
এই হইহুল্লোড় হাসাহাসিতে পেটেরটা হজম হয়ে যায়। তখন আবার পরিবেশন চলতে থাকে। এর কারণ, এই প্রসাদ কেউ পাতে ফেলতে পারবে না, আবার সম্পূর্ণ পেট না ভরে খেলেও চলবে না। তাতে নাকি বংশে কলেরা হওয়ার সম্ভাবনা আছে, অন্তত এর পরবর্তী ছড়াটি তো তাই বলে।
গ্রামের দক্ষিণে গভীর জঙ্গল। সেখানে ছোটো-বড়ো এলোমেলো ছায়াঘন গাছের অন্ত নেই। জায়গাটিকে বলে ‘পরান শীলের বাড়ি। এখানে প্রাচীন হরীতকী গাছের তলায় মস্ত উইটিপি আর আশপাশে ঘুরে ঘুরে পাহারা দেয় মস্ত মস্ত সাপ। কোন কালের সঞ্চিত ধনসম্পত্তি নাকি আছে ওই উইঢিপির মধ্যে। বর্ষাকালে এখানে বড়ো বড়ো বাঘের থাবার চিহ্ন পড়ে।
শীত আসে। শেষরাত্রে পাতায় পাতায়, টিনের চালের এখানে-ওখানে থেমে থেমে, মোটা মোটা টুপ টাপ টং টং শিশির ঝরার শব্দ শোনায়। ঘাসের শিশিরে দু-পা ভিজে যায়। নীরব সন্ধ্যায় ল্যাজঝোলা ‘শিয়ালি’ কোথায় যেন টুক টুক টুক টুক করে খেজুর গাছ কাটে! খালের স্বচ্ছ জলে গাছের সারি চুপচাপ মুখ দেখে, আর কেউ কোনো নৌকা বেয়ে গেলে তাদের ছায়াগুলো যেন খিলখিল করে হেসে ওঠে। ক্রমে রাত্রি হয়, মাঝে মাঝে ‘আওলা দানো’ বা আলেয়া ভূত নামে।
শীতের মাঝামাঝি গ্রামে বাঘ-পুজো হয়। জঙ্গলের পথে পথে সন্ধের পর মশাল জ্বেলে ছেলে-মেয়েরা বেরোয়, আর বুধাই শীলের পাঠশালার নামতা পড়ার মতো সুর করে একজন আগে বলে ও পড়ে আর সবাই—
আইলাম রে শরণে,
লক্ষ্মীদেবীর বরণে,
লক্ষ্মীদেবী দিলেন বর,
চাউল কড়ি বিস্তর।
চাউল না দিয়া দিবেন কড়ি,
ঠিক দুয়ারে সোনার লরি;
সোনার লরি রূপার মালা,
পাঁচ কাঠালে সোনার ছালা।
একটি টাকা পাই রে–
বানিয়া বাড়ি যাই রে।
এর পর তারা বারো বাঘের ছড়া বলে,
এক বাঘ রে এক বাঘ রাইঙ্গা,
ঘর ফালাইল রে ঘর ফালাইল ভাইঙ্গা;
আর বাঘ রে আর বাঘ চৈতা,
বাওন মারইয়া রে বাওনের নিল পৈতা,
আর বাঘ রে আর বাঘ নৈচৈ
গোয়াল মারইয়ার গোয়াল মাইরা খাইল দই।–ইত্যাদি।
পুজোর দিন উঠোনে, বড়ো বড়ো বাঘা-বাঘিনি এঁকে মেয়েরা হলুদগুঁড়ো চালগুঁড়ো সরষে কালোজিরে–এসব দিয়ে বাঘের গা করত চিত্ৰবিচিত্র। সে-দিন ঘরে ঘরে আলো জ্বালা হত না। সবাই পুজোর চিড়ে পেটভরে খেয়ে রাত কাটাত।
কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোর দিন এবাড়ির ওবাড়ির মা কাকিমা বউদি বোনদের সারাদিন উপুড় হয়ে ঘরজোড়া রুচিশুভ্র আলপনা দেওয়া দেখতাম। দেশের মা দুর্গার কী টানা টানা চোখ! আমরা কুমোরদের বলি ‘গুণরাজ’। আমাদের জানকী গুণরাজ কালা। জোরে না বললে সে শোনে না, কিন্তু কথা নিজে বলে খুবই আস্তে। সে এমনি কাটা মোষের মাথা তৈরি করে উঠোনে রাখত যা দেখে শকুনি উড়ে পড়ত। নিজের হাতের কনুইয়ের কাছটা ঠোঁটে লাগিয়ে জানকী ইশারায় তামাক চাইত। পুলঘাটায় গুণরাজের মাটির নৌকো আসে। সেখানে ছেলেদের কী জমাট জমায়েত। পুলের কাছেই বোসেদের দিঘি আর হাটখোলা। দূরে দূরে কলাপাতার ঘোমটাটকা লাজুক সব কুটির। ও-পাড়ে ময়াল সাপের মতো শেকড়-জড়ানো ভ্রূকুটি-কুটিল বাদামগাছের ডালে ডালে শকুনিরা চোখ বুজে ঝিমোয়। বাড়ি আসার সময় এখানে নেমে কোনো গ্রাম্য বৃদ্ধকে দেখে প্রণাম করতে হত। এখানে নেমেই মনের পর্দায় ভেসে ওঠে,–মা ভিজে চুল পিঠে মেলে উনুনে ফুঁ দিচ্ছেন। কাকিমা আর বউদি টেকি পাড় দিতে দিতে হাসছেন। পিসিমা উঠোন ঝাঁট দিতে দিতে সবে কোমর সোজা করে দাঁড়ালেন, সোনাভাই দাঁতহীন ঠোঁট নেড়ে পুকুরের জলে জবাফুলের পর জবাফুল ভাসিয়ে চলেছেন, কামিনী আর স্থলপদ্ম গাছের ফাঁকে ফাঁকে। আমাদের কোথাও যাত্রাকালে এই পুলঘাটা অবধি ঠাকুরদাদা মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে আসতেন–’ধেনুর্বৎস প্রযুক্তা, বৃষগজতুরগা দক্ষিণাবর্ত বহ্নি’…
চা খাওয়ার রেওয়াজ আমাদের গ্রামে নেই। কিন্তু প্রত্যেক বাড়ির বাইরের বারান্দায়, এক তাওয়া আগুন, একতাল তামাক, কয়েকটি করে কলকে আর কো–এ থাকবেই। তাওয়াটিতে চব্বিশ ঘণ্টাই আগুন থাকে। মেয়েরা গন্ধক কাঠি তৈরি করে রাখে এবং দেশলাইয়ের পরিবর্তে ওই গন্ধক কাঠির সাহায্যে তাওয়ার আগুনে আলো জ্বালানোর কাজ চলে।
অতিথিপরায়ণতা গ্রামবাসীদের মজ্জাগত। কৃচিৎ কোনো লোকের সঙ্গে দেখা হলে তার চোদ্দো-গোষ্ঠীর সংবাদ জিজ্ঞেস করা এদের স্বভাব। নেহাত অতিথি হিসেবে সে যদি নাও থাকতে চায় অন্তত একছিলিম তামাক তাকে খেতেই হবে। ভাড়ার নৌকোকে আমাদের ওদিকে বলে ‘কেরায়া নাও”। এই কেরায়া নাও-এর যাত্রীদেরও এ ব্যাপারে রেহাই নেই। এসব মনগুলো শহর কলকাতায় এসে যে কী অবস্থায় পড়ে কী রূপ পরিগ্রহ করবে, তা ভাবতে গিয়ে থেকে থেকে একটা কান্নার দমকা আমার বুক-গলা পর্যন্ত ঠেলে ওঠে, চোখ ভিজে আসে।
সেসব থেকে থেকে পাখি-ডাকা গভীর রাত্রের নীরব শিহরন আর আমাদের কানে আসবে না। ‘অক্কু’র ডাকে ডাকে রাত্রির যাম আর গুনতে হবে না। চিলের মতো এক প্রকার পাখি অকু। পুকুর পাড়ের উঁচু তালগাছে থাকে। ঝড়-ঝঞ্ঝা বাদল-বৃষ্টি যাই হোক-না-কেন সন্ধের পর থেকে প্রতি চার প্রহর পর পর এরা ডাক শোনাবেই। এদের কণ্ঠ সবার ওপরে। দিনের বেলা ছায়া মেপে সময় নির্ণয় করার প্রথা আমাদের ওদিকে বিশেষ প্রচলিত। ছায়া মেপেই ঘড়ি ঠিক রাখতে হয়।
পদেতে মাপিলে ছায়া যত পদ হবে,
দ্বিগুণ করিয়া তাহে চৌদ্দ মিশাইবে।
এর পরের লাইন দুটি মনে নেই, তাতে বিশেষ ক্ষতিও নেই। ছায়া যত পা, তাকে দুই দিয়ে গুণ করে চোদ্দো যোগ করে তাই দিয়ে ২৯২কে ভাগ দিলে দন্ড হয়, আড়াই দন্ডে এক ঘণ্টা।
সাম্প্রদায়িক গোলযোগ আমাদের গ্রামে কোনোকালেই ছিল না, আজও নেই। প্রথম দাঙ্গা আরম্ভের পর, কলকাতার খবর পেয়ে আমাদের গ্রামে গ্রাম্যভাষায় সত্যপীরের পাঁচালির সুরে ছড়া লেখা হয়েছিল। পাঁচালিটি বেশ বড়ো সুতরাং মাঝখান থেকেই একটু বলি,
তোমার ঘরে পানি নেওনা আমি যদি ছুঁই,
গো-জবাইতে বাধা দিলে কাফের কইতাম মুই।
অশিক্ষা কুশিক্ষা আলহে তোমাতে আমাতে
তমো মোরা দুইজনেই আলহাম হাতে হাতে।
রাজায় রাজত্ব হরে পেরজার চৌহে ঝরে পানি,
অধর্মেরই ছুরি খাইয়া অইলাম রে অয়রানি।
তবু সে আজ আমাদের ছেড়েআসা গ্রাম। সে-গ্রাম ছেড়ে আসতে পা কি চলতে চায়, বার বার পেছন ফিরে ঝাপসা চোখে চেয়ে চেয়ে দেখেছি, কেবল দেখেছি। দু-একজন মুসলমান প্রজা সঙ্গে সঙ্গে স্টেশন অবধি এসেছিল। খালাসিরা সিঁড়ি ফেলল। ওপারে ধানের খেত। নৌকাগুলো ঢেউয়ের আঘাতে আছাড় খাচ্ছে, মাঝিদের কোলাহল, সন্ধে আকাশে একঝাঁক পাখি কোথায় উড়ে গেল, দিগন্তে পান্ডুর সূর্যাস্ত। কেঁপে কেঁপে স্টিমারের বিদায়ের বাঁশি বেজে ওঠে। ঘাট নোঙর ছেড়ে দেয়। দু-ফোঁটা চোখের জল, বুকভরা অশান্ত কান্না। তারপর শহর। এখানে আমরা যেন কোনো ভিন্ন জাতি, সভ্যতার একটুকু বিলাসবসনের চিহ্ন যাদের দেহে নেই, তাদের সারামুখে দেখা দেয় একটা অপমৃত্যুর বিভীষিকার ছায়া। আর সেখানে দু-শো বছরের পুরোনো বটকে যেন কেউ সমূলে উপড়ে ফেলেছে, সেখানে খাঁ খাঁ করে একটা বিরাট শূন্যতার গহর। সেখানকার সন্ধের নিশাচর বাদুড়েরা গ্রামের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে যেতে আর কোনো কচি কচি গলার সুরে শোনে না,
বাদুড় ভাই, বাদুড় ভাই, তুমি আমার মিতা,
আমারে ফেলাইয়া যে ফল খাবা,
সে ফল তোমার তিতা তিতা তিতা!
সত্যি, আমার গাঁয়ের প্রিয় পশুপাখিরা কীভাবে আমাদের কথা, তারা কি আজও মনে রেখেছে আমাদের? আমরা যে কিছুতেই ভুলতে পারি না তাদের, ভুলতে পারি না আমার গাঁয়ের সে মাটি, সে জল, সে গাছপালা ও সে মিষ্টি বাতাসকে! আবার কবে ফিরে যেতে পারব তাদের মধ্যে?
.
নলচিড়া
‘মোট ক্ষতির পরিমাণ কত?’ প্রশ্ন করেছেন সরকার। উদবাস্তু শরণার্থীদের ছেড়ে-আসা ভিটেমাটিতে মোট ক্ষতির পরিমাণ কত তা জানাতে হবে সরকারকে। গণিতের হিসেবে চিরকাল আমি কাঁচা। সাহায্য নিয়েছিলুম কোনো বন্ধুর। সত্যি, কত নম্বর মৌজায়, কত নম্বর খেবটে আমার কী ধরনের স্বত্ব, সে-খবর কোনোদিন রাখিনি। আমার সম্পত্তির অবস্থান এবং আমার স্বত্ব বোঝাতে গেলে যতখানি জ্ঞানবুদ্ধি প্রয়োজন, আমার তা কোনোদিনই ছিল না। কিন্তু গোটা নলচিড়াকে এত ভালো করে চিনি যে তার সম্পর্কে কিছুমাত্র ভুল হয় না।
আড়িয়ালখাঁর দক্ষিণ তীরে সাহেবের চর থেকে আমাদের এই গ্রামের পত্তন। সদর থেকে মাইল কুড়ি উত্তরে। পড়শি গ্রামের সঙ্গে আমাদের সীমানা ছোটোখাটো নিশানা দিয়ে। আমাদের গ্রাম থেকে মাহিলাড়া পেরিয়ে অশ্বিনী দত্তের বাটাজোড় মাইল পাঁচেক হবে। অনেক উপলক্ষ্যেই যাওয়া হত সেখানে। সবচেয়ে উৎসাহ পেতাম লক্ষ্মীপুজোর দিন জলপদ্ম আনতে গিয়ে। জেলাববার্ডের সড়কে দু-মাইল এগিয়ে একটা সোতা পেতুম। পার হয়ে বলতুম, পৌঁছোলাম ভিন গাঁয়ে। এমনি সব সীমানা।
একেবারে অচিন গাঁয়ের অধিবাসী আমরা নই। তিমির তীর্থের সাহিত্যিক যে দেশের মাটিতে প্রণাম রেখেছেন, সে আমাদের সবার তীর্থভূমি। বাইরের সঙ্গে তাঁর গ্রামকে একালে তিনিই যুক্ত করে দিয়েছেন। আমাদের ইতিহাসের কথা আমরা মুখে মুখে রক্ষা করেছি। সংস্কৃতচর্চার একটি কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল নলচিড়া। এক ভটচায্যি বাড়িতেই চোদ্দোটি টোল ছিল। নবদ্বীপে না গিয়ে অনেকে আসতেন এ গাঁয়ের দিগবিজয়ী পন্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কাছে। বিশেষ করে তাঁরই গৌরবে নলচিড়া ‘নিম্ন-নবদ্বীপ’ বলে খ্যাতি পেয়েছিল। গোটা গোটা আমলকীর লোভে আমরা যেতুম ‘নাক কাটা বাসুদেব’-এর বাড়ি। ও বাড়ির পুকুর পাড়ে একটি খন্ডিত বাসুদেব মূর্তি ছিল। শুনেছি নলচিড়ার এমন আরও কয়েকটি শিলামূর্তি এবং শিলালিপি ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত হয়েছে। এসব অতীত ইতিহাস নিয়ে গৌরব করতাম। কিন্তু যে ক্ষতি সহ্য করছি তা প্রকাশের মতো ভাষা কোথায়? আমাদের সর্বাঙ্গে মাখানো থাকত গ্রাম-মায়ের স্নেহের পরশ। এখনও মাঝে মাঝে হাবার মতো কলকাতার রাজপথে তাই খুঁজে খুঁজে বেড়াই।
সদর থেকে ডিঙিনৌকা অবশ্য বাড়ির ঘাটেই পৌঁছে দিত। কিন্তু ‘গয়না’-র নৌকা দাঁড়াত শিববাড়ি ঘাটে। সমস্ত গ্রামখানার মধ্যে এই এলাকাটুকুরই একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। একটি শিবমন্দির, খানকয়েক মুদি দোকান, একটি ডাকঘর এবং একটি পাঠাগার। এর যেকোনো একটিকে উপলক্ষ্য করেই গাঁয়ের লোক এখানে জড়ো হতেন, রসিকজন বিনা উপলক্ষ্যেও আসতেন। শিবমন্দিরটির মূলকাঠামো জ্যান্ত বটগাছের না ইটপাথরের বোঝা যেত না। ছেলেদের বসবার জায়গা ছিল ওর ফলন্ত ডালগুলো আর না হয় গাছটার বাড়ন্ত শিকড়গুলো। বুড়োরা এ খালপারের তেঁতুল গাছটিকে নিষ্ফলাই বলতেন। ছেলেদের দৌরাত্মে এর ফলের মাহাত্ম্য তাঁরা টের পেতেন না। মুদি দোকানের বৈঠক কখনো ক্ষান্ত হতে দেখিনি। গ্রামের সালিশি থেকে আরম্ভ করে কীর্তনের মহড়া সবই চলত এইখানে। গ্রামের সব কথার মোহানা এই শিবতলায়। বিকেলের দিকে অনেকে বসতেন পাঠাগারের সামনে। দু-দিনের বাসি খবরের কাগজ পৌঁছোত। আর তাই নিয়েই চলত যত পঠনপাঠন সমালোচনা।
মহেন্দ্রস্মৃতি পাঠাগারের বর্তমান বয়েস বারো-চোদ্দো বছরের বেশি নয়। গ্রাম ছেড়ে আসার দিনও দেখেছি হাজার দেড়েক বই এবং আনুষঙ্গিক সব কিছু নিয়ে সার্থক হয়ে উঠেছে। পাঠাগারটি। কোনো বিশেষ একজন এ প্রতিষ্ঠান গড়ে দেননি, এটি ছিল সর্বজনের হাতে গড়া। একে কেন্দ্র করেই আমরা ছেলের দল গ্রামের রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখতুম, ছোটোখাটো সড়ক বাঁধতুম। ছোটোবেলা থেকেই ‘সরকারের দিঘি’-র পাড়ে জঙ্গলের মধ্যে একটা ‘কঙ্কালঘর’ দেখতুম। এটাই ছিল বিবেক আশ্রম। শংকর মঠ’-এর আদর্শে ধর্মচর্চার জন্যে এর পত্তন করলেন শচীন কর। তারপরে এল শরীরচর্চা। তারপর সারাদেশের সঙ্গে সৎ ও শক্ত আশ্রমবাসীরা দীক্ষা নিলেন অগ্নিমন্ত্রে। রায়ের ভিটা’-র জঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত হল মহেন্দ্র রায়ের বোমার উৎসভূমি। এর পরের কাহিনি গল্পের মতো। শেষপর্যন্ত মহেন্দ্র রায় ধরা পড়লেন মেছোবাজার বোমার মামলায়। কারাগৃহেই তাঁর প্রাণ গেল। …একদিন হঠাৎ স্কুলের মাঠ থেকে সবাইকে তাড়িয়ে নিয়ে এলেন মন্তুদা ‘সরকারের দিঘি’-র পাড়ে। কাঠামোটা না ভেঙে আমরা সবসুদ্ধ আশ্রমগৃহটি মাথায় করে নিয়ে এলুম শিববাড়ি। এ দৃশ্যটি আজও মনে পড়ে। এইটেই আমাদের মহেন্দ্র পাঠাগার। বড়ো পাঠাগার আরও দুটি আছে–একটি নিম-নদিয়া গ্রন্থাগার আর একটি ইউনিয়ন বোর্ডের লাইব্রেরি।
এখন আর একটি কথা ভাবতে বুকটা ফুলে ওঠে। আমাদের চন্ডীমন্ডপে একটি খুঁটির সঙ্গে বড়ো একটা পেরেক ছিল। ন্যাশনাল স্কুলের ব্ল্যাকবোর্ড টাঙানো হত ওইখানে। দুর্গাঠাকুর রং করবার সময় সমস্ত রঙের সেরা রক্তচিহ্ন রেখে দিতুম ওই পেরেকটির চারদিকে একেবারে ছোটোবেলা থেকে। দশভুজার মন্ডপে ওই শক্ত মানুষগুলোকেই মানাত।
ডাকঘরের কথা বলছিলুম। আমরা ছোটোবেলা থেকে ওই ঘরটি একজনের তত্ত্বাবধানেই দেখেছি। এর ‘প্রবেশ নিষেধ’-এর সতর্কবাণীটি অনেককালই মুছে গিয়েছিল। দেখো তো মাস্টার’, বলে মনি অর্ডার প্রত্যাশী অনেকেই ঘরে ঢুকে পড়তেন। ঘরের কর্তা আপত্তি করতেন না।
শিববাড়ির কাছেই নলচিড়া স্কুল। পাশাপাশি চারটি গ্রামের ছেলেদের নিয়ে এ অঞ্চলে এই প্রথম ‘হাই স্কুল স্থাপিত হয়েছিল। প্রায় চল্লিশ বছর আগে ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তারপর অবশ্য আলাদা আলাদা স্কুল হয়েছে। আমাদের আমলে বিজ্ঞান আবশ্যিক পাঠ্য হল। উদ্ভিদ এবং প্রাণীবিদ্যার আংশিক সরঞ্জাম গ্রামেই জুটে গেল। পদার্থ রসায়নের কিছু যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের তাগিদে। সারাবছর ধরে দেখলাম ওর আলমারি তালাবন্ধই থাকল চাবি খারাপ বলে। ওর একটা জিনিস নষ্ট হলে নলচিড়া স্কুলের পক্ষে যে ভারি বিপদের কথা!
‘সরকারের দিঘি’-র উত্তর-পূর্ব কোনায় জলের মধ্যে অবিরত বুদবুদ উঠত। ওই নিয়ে অনেক কাহিনি আমরা ছেলেবেলায় শুনতাম। তারপর স্কুলে নলকূপ বসাতে গিয়ে গন্ধকের সন্ধান পাওয়া গেল মাটির তলায়। নলকূপের গর্তটার মুখে ফুটো সরা বসিয়ে দেশলাই জ্বেলে দিতুম। খুব জোরে হাওয়া না দেওয়া পর্যন্ত নীল আলো জ্বলত। শাপলার ডাঁটা দিয়ে ওই আলো আমরা স্কুল অবধি নিয়ে যেতুম। অক্সফোর্ড গ্র্যাজুয়েট বিমলদা আমাদের সব পাগলামোর বুদ্ধি জোগাতেন। ভূতুড়ে ব্যাপারটির কিছু হদিশ মিলল বটে। কিন্তু খুব আতঙ্ক এল সবার মনে। গন্ধকের খনি ফেটে নলচিড়া উড়ে যাবে, নয়তো সরকার গন্ধক তুলতে গিয়ে গ্রাম উঠিয়ে দেবেন। বৃদ্ধদের পরামর্শে গর্তের মুখে মাটি চাপা দিতে হল।
আমাদের বাঁশতলার নতুন আমগাছে আষাঢ় মাসে ফল ধরল। জ্যাঠাইমা প্রথম ফলটি দিয়ে পাঠালেন কুতুব শার দরগায়। বড়ো হয়ে দেখেছি গ্রামসুদ্ধ লোক প্রথম ফসল উৎসর্গ করেন ওই দরগার কুতুব শার আশীর্বাদ প্রার্থনা করে। ওই দরগায় একখানা পাথরখন্ডের তলা থেকে কুতুব শার আজান শুনতাম আমরা। কাজে-অকাজে আমাদের ডাক পড়ত। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় ওই দরগায় বিরাট মেলা বসত। খেতের ফসল, গাছের ফলমূল, গাই-এর দুধ, যে-যেমন পারত নিয়ে আসত। সব মিলিয়ে জ্বাল দেওয়া হত বিরাট একটা মাটির পাত্রে। ওই প্রসাদ সবাই নিত অসংকোচে। বিজয়া এবং রাসপূর্ণিমার পরদিন ‘সন্তেশ (সন্দেশ)-কলা’ পেতে এবং রাধাকৃষ্ণের দেহাবশেষ’ কুড়োতে আসত হিন্দু-মুসলমান সব ছেলে-মেয়ে।
প্রত্যক্ষ দেবতার ঠাঁইতে পৌঁছেলেই হাতদুটো আপনার থেকেই যুক্ত হয়ে আসত। ঠাকুরের খোলা, রক্ষাচন্ডীর খোলা, হরগৌরীর ভিটে এসবের কথা মনে দাগ কেটে আছে। দেবীদাস বকসির কালীমার ভোগের ‘পাথর’ পুকুরে পড়েছিল কয়েক পুরুষ আগে। পুকুর। সংস্কার করতে গিয়ে এক এয়োতির হাতে পড়ল ওই থালা। মা স্বপ্ন দেখালেন। মানল না ও। তিনরাত না পোয়াতে পরিবারসুদ্ধ নিশ্চিহ্ন হল! প্রতিটি দেবতাকে কেন্দ্র করে এমনি সব অতীত ও চলতি কাহিনির অন্ত ছিল না। অলীক হলেও এসবে লোকের অবিশ্বাস নেই!
‘কালীসাধক মঠে’-র ঠাকরুনকে ভারি ভয় করতুম। বাড়িতে এলে মাঝ উঠোনে উনি বসতেন। বাড়িসুদ্ধ লোক পায়ে পড়ে প্রণাম করতাম। ছোটোবেলা থেকে ওঁকে একইরকম দেখেছি। মাঝে মাঝে ওঁর শিষ্যদের কাছে আমাকে দিয়ে চিঠি লেখাতেন। অরণ্যে রোদন’ কথাটি ব্যবহার করতে হত অনেকবার।
ঠাকরুনের কালীসাধনার গান শুনে ভয় লাগত। কিন্তু লক্ষ্মীকান্তের পদাবলি গান আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। ওঁর চওড়া বুকখানায় অনেকগুলো পদক শোভা পেত। বাংলার জেলায় জেলায় তিনি সম্মান পেয়েছেন। গ্রামে একবার ওঁর কীর্তন হলে অনেকদিন ধরে আমাদের মুখে মুখে তার অনুসরণ চলত-শোনো বুড়িমাই, তোমাকে জানাই আমার মরম কথা। লক্ষ্মীকান্তের মৃত্যুর পরেও এই কীর্তনের দল ভেঙে যায়নি। এই সঙ্গে মনে পড়ে বৈকুণ্ঠ ঢুলিকে। কোনো এক উৎসবে মাছরঙের বিখ্যাত বাজনদাররা এসেছেন। আসর খুব জমে উঠেছে। বৈকুণ্ঠ ঢুলি হাতজোড় করে বললেন,–একটি টোকা কম পড়ছে। পরে দেখা গেল ওর বাঁ-হাতের একটি আঙুল কাটা। পরদেশি বাজনদার গুরু বলে মেনে নিল বৈকুণ্ঠকে। ভ্রমর বয়াতির জারিগান শুনতে চারপাশের গ্রাম পর্যন্ত ভেঙে পড়ত। বাঁশের সাঁকো সেদিন শিথিল হয়ে যেত।
কালী পুজোর পর দু-দিন ধরে দত্তবাড়ি এবং পালবাড়িতে যাত্রাগান হত। ভোরে উঠে আগের দিনের প্রসাদ নিয়ে হাজির হতুম। দু-বাড়ির আসর এবং সাজঘর সব আমাদের দেখা চাই। আসরের মহারানি সাজঘরে বিড়ি খাচ্ছেন, এইটে দেখার খুব আগ্রহ ছিল আমাদের। আমাদের গ্রামেও যাত্রার দল ছিল। প্রথম অভিনয়ের পরেই ওর অভিনেতাদের নতুন নামকরণ হয়ে গেল। পুজোর পর কালীপুজো অবধি পর পর থিয়েটার চলত। ওই কটা দিন গ্রাম থাকত কোলাহলমুখর! প্রবাস থেকে আসত মানুষ, মফসসলের জমিন থেকে আসত ফসল।
রাধা করাতির নীল পুজোর গান আমাদের মুখস্থ ছিল। মহাদেব-গৌরীর পেছন পেছন আমরা ছুটতুম এই বলে,–‘শঙ্খ পরিতে গৌরীর মনে হইল সাধ।’ সন্ন্যাসের দিন আমাদের আনন্দের সীমা থাকত না। বাস্তুপুজো উপলক্ষ্যে আমরা গান গেয়ে ভিখ নিতুম—’আইলাম লো শরণে, লক্ষ্মীদেবীর বরণে।’ ‘বারোবাঘের লেখাপড়ি’ আমরা খুশিমতো রচনা করতুম। সারাবছর যাঁদের ওপর রাগ থাকত বাঘ বানাতুম তাঁদেরই। দোলপূর্ণিমার আগের দিন ‘বুড়ির ঘর’ পোড়ানো ছিল সবচেয়ে মজার ব্যাপার। সহজদাহ্য সব কিছু লাগত আমাদের এ ‘উৎসবে’। বাগান সাফ হয়ে যেত। বুড়ির ঘরের উচ্চতার পাল্লা দেখে বৃদ্ধরা শিউরে উঠতেন, বলতেন, ‘শেষে এক কান্ড বাধিয়ে বসবি!’
চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে সপ্তাহখানেক ধরে বিভিন্ন জায়গায় মেলা বসত। মেলা বুঝে আমাদের ‘থৌল-খরচ’ বরাদ্দ ছিল। দক্ষিণপাড়ায় কালীতলার মেলায় মা-জ্যাঠাইমারাও যেতেন। বছরের মশলাপাতি কেনা হত ওইখানে। বছরের পয়লা আমাদের একটা বার্ষিক কর্ম ছিল। গানের বৈঠক বসত।
দেশভাগের কয়েক বছর আগে কলকাতায় নলচিড়া সম্মিলনী গ্রামের সমস্ত কল্যাণকর্মের দায়িত্ব নিল। ষোলো বছর পর জেল থেকে বেরিয়ে শচীন কর সংগঠনের কাজে লেগে গেলেন। সাহেবের চরের বিশ্রামাগার, মেয়েদের হাই স্কুল, মেয়েদের কংগ্রেস, কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্র সব গড়ে উঠল। ভেঙেও পড়ল সব কটি বছরের মধ্যেই! রাষ্ট্রদ্রোহী’ শচীন করকে যথাকালে পালিয়ে আসতে হল। স্কুল বিল্ডিং ফাণ্ডের টাকা সেদিন ফিরিয়ে দেওয়া হল। একটি অবৈতনিক পাঠশালা গড়ে উঠেছিল। মাস কয়েক ওতে পড়িয়েছিলুম। ছুটির সময় হলে ছেলেরা বলত, ‘মাস্টারমশায়, জল খেয়ে আসি-ই।’ সে স্মৃতিটুকু সোনা হয়ে রয়েছে।
দেশভাগের পরেও অনেকদিন আদর্শ পাঠশালা, মহেন্দ্র-স্মৃতি পাঠাগার এবং রেডক্রস নিয়ে মেতেছিলুম। একদিন তাড়াহুড়ো করে সব ছেড়ে চলে আসতে হল। সন্ধেবেলা এলাম সাহেবের ঘাটে। স্টিমার এল শেষরাতে। অতক্ষণ আমি কী করেছি? সে সময়কার মনের অবস্থার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। বোধহয় ফাঁসির আগের রাতে অমন হয়।
সেদিন কলকাতায় আমাদের গ্রামের পোস্টমাস্টারমশায়ের সঙ্গে দেখা! উনি আমাদের স্কুলেরও মাস্টার ছিলেন। এক কোম্পানিতে কেরানির কাজ করছেন এখন। সেদিন ওঁর অফিসে গিয়ে দেখি পুরোনো সমস্ত কাগজপত্রে লাল কালির দাগ দিয়ে রেখেছেন, বললেন,–ইংরেজি ভুল। ডিগ্রিবিহীন এ সনাতন শিক্ষকটির স্থান কোথায়?
অগোছালো কথা এখানেই শেষ করি। …বেশি ভাড়া দিয়ে একদিন এক্সপ্রেস বাসে ওঠা গেল। প্রচন্ড বর্ষা। এমনিতেই সতর্কবাণী–বাইরে হাত দিয়ো না। সাবধানিরা জানলার কপাট তুলে দিলেন। ইচ্ছে করেই দাঁড়ালুম পা-দানির ওপর। হঠাৎ একটা স্মৃতির বিদ্যুৎ খেলে গেল মনের আকাশে ভাদ্রমাসে একটা ভরা খাল দিয়ে বাইচের নৌকা বেয়ে চলেছি। বাঁ-হাতে আর পায় ঠেকিয়ে বইঠা, ডান হাতে টেনে তুলছি কলমি শাকের ফুল। বুকটা মোচড় খেয়ে উঠল। অবাক হয়ে ভাবলুম, তাহলে আমার মোট ক্ষতির পরিমাণ কত?
ভূমিকা ও প্রকাশকের নিবেদন – ছেড়ে আসা গ্রাম
সমগ্র বঙ্গদেশ ও বাঙালিকে যাঁরা ভালোবাসেন তাঁদের হাতে
.
প্রকাশকের নিবেদন
ছিন্নমূল মানুষের দুর্বিপাকের কাহিনি নতুন কিছু নয়। সেই মোজেসের কিংবদন্তি থেকে শুরু করে মায়ানমারের রোহিঙ্গাদের ভাগ্যবিপর্যয় অবধি এই ট্র্যাজেডি বহমান। কিন্তু ছিন্নমূল তামিল অথবা ইহুদিদের নিয়ে ইতিহাস যতটা উদবিগ্ন, ততটাই উদাসীন খন্ডিত বঙ্গদেশের উৎপাটিত বাঙালি সম্পর্কে।
১৯৪৭-এর দেশবিভাগ বাঙালি জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা। ১৯৪৭-১৯৫০ এই তিন বছরে এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পরেও প্রত্যেক বছরে যেভাবে লক্ষ লক্ষ বাঙালি বঙ্গদেশের পূর্ব অংশ থেকে পশ্চিমাংশে চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন, বিতাড়িত হয়েছেন, তার প্রকৃত ইতিহাস আজও লিপিবদ্ধ হয়নি। শুধু ভারতবর্ষের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও এমন মর্মন্তুদ অপসারণের উদাহরণ আর নেই।
সীমান্তের অপর পারে, নতুন দেশে, তাঁরা হারালেন অতীত স্বীকৃতি, সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ পড়ে রইল স্মৃতি–যে স্মৃতি অশ্রুসজল। শুধু ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে আসার বেদনা নয়, তাঁদের হৃদয় শোকসন্তপ্ত হয়ে রইল প্রিয়জনকে চিরকালের মতো ছেড়ে চলে আসার দুঃসহ কষ্টে।
দক্ষিণারঞ্জন বসু প্রণীত এই গ্রন্থ পূর্ববঙ্গের আঠারোটি জেলার চৌষট্টিটি গ্রাম থেকে ভূমিপুত্র-কন্যাদের চলে আসার বৃত্তান্তকে ধরে রাখার চেষ্টা করেছে।
গ্রন্থের দুটি খন্ড প্রকাশিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল তদানীন্তন পাকিস্তানে। পরে জিজ্ঞাসা দুটি খন্ডকে একত্রিত করে ১৩৮২ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করে। এর চল্লিশ বছর পর এই ২০১৫ সালে পারুল প্রকাশনীর উদ্যোগে পুনঃপ্রকাশিত হল এই মহাগ্রন্থ। তাৎপর্যমন্ডিত এই পুনঃপ্রকাশ নিঃসন্দেহে স্মৃতিমেদুর করে তুলবে পশ্চিমবঙ্গ ও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ–উভয় বাংলার বাঙালিকেই।
.
ছেড়ে আসা গ্রাম
সুখের কথা, অসংখ্য পাঠকের দীর্ঘদিনের ক্রমাগত একটি চাহিদা এতকাল পরে পূরণ করা সম্ভব হল। বিখ্যাত প্রকাশনী সংস্থা ‘জিজ্ঞাসা’ দুই খন্ডের ছেড়ে আসা গ্রাম গ্রন্থটি বহুজনের অনুরোধে একসঙ্গে প্রকাশ করে বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমগ্র বাঙালি পাঠকসমাজের ধন্যবাদভাজন হলেন।
শুধু পশ্চিমবাংলাই মূল বঙ্গদেশ নয়। বাঙালির ইতিহাসও শুধু পশ্চিমবাংলার ইতিহাস নয়। অনেক বড়ো তার পটভূমিকা, অনেক ব্যাপক তার বিস্তার। মূল বাংলার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গ বাকি দুই-তৃতীয়াংশ অন্য দেশ-ভারত-দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আর এক রাষ্ট্রের পূর্বাংশরূপে তার নতুন নাম হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান। সত্তর দশকের গোড়ায় পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ববঙ্গ এখন অবশ্য স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ বলে পরিচিত। তাহলেও সে পৃথক রাষ্ট্র, ভিন্ন শাসনব্যবস্থায় সে-দেশের বাঙালিরা পশ্চিমবঙ্গ থেকে একরূপ বিচ্ছিন্ন। কিন্তু ভাবীকালের বাঙালির কাছে পল্লিহৃদয় বাংলার পূর্ব সত্যরূপ, তার সত্যকারের পরিচয় তুলে ধরার দায়িত্ব কি আমাদের নয়? এই প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতেই আমি ‘ছেড়ে আসা গ্রাম’ সম্বন্ধে নানা কাহিনি সংগ্রহের পরিকল্পনা করেছিলাম দেশবিভাগের অব্যবহিত পরেই। সহযোগিতাও পেয়েছিলাম আশাতীত।
১৯৪৭ থেকে ১৯৫০। বাঙালির চরম দুঃসময়ের সে-কাল। সেই পঞ্চাশের বেদনাঘন দুর্দিনে যুগান্তর-এ যখন ছিন্নমূল পূর্ববঙ্গীয় উদবাস্তু নর-নারীর কাছ থেকে সংগৃহীত ছেড়ে আসা গ্রামের মর্মন্তুদ আলেখ্যসমূহ প্রকাশিত হতে থাকে তখন দেশবাসীর মধ্যে এক তীব্র তুমুল আলোড়ন দেখা দিয়েছিল। সেইসব কাহিনির মধ্য দিয়ে অভিশপ্ত খন্ডিত বাংলার পূর্বপ্রান্তের সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-হতাশাজড়িত ইতিহাসকে ভাষায় রূপায়িত করা হয়েছিল। তার প্রধান লক্ষ্য ছিল, ইতিহাসের বিচ্ছিন্ন ধারাকে কথায় ধরে রাখা, ভবিষ্যতের মানুষ যাতে ‘বাঙালি’ বলে পরিচিত একদল মানুষেরই ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের ছিন্নসূত্রটুকুর সন্ধান লাভ করতে পারে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে, শুধু ভারতবর্ষেরই বা কেন, পৃথিবীর ইতিহাসেও কোনো দেশে এরূপ ব্যাপক বাস্তুত্যাগের নজির পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। একটা
দেশের লক্ষ লক্ষ সুখী শান্তিপ্রিয় মানুষ তাদের পিতৃ-পিতামহের পুণ্য স্মৃতিজড়িত বাস্তুভিটে, অভ্যস্ত জীবনযাত্রা, পরিবেশ ও সংস্কৃতিকে বিসর্জন দিয়ে সম্পূর্ণ উন্মুলিত হয়ে রাজনৈতিক ঝঞ্ঝায় ঝরাপাতার মতো উড়ে এসে পড়ল সীমান্তের অপর পারে, অন্য রাষ্ট্রে। তাদের না রইল অতীত স্বীকৃতি, না রইল স্থির ভবিষ্যৎ। মানুষের ইতিহাসে এর চেয়ে মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি আর কী হতে পারে? এই বেদনা থেকেই ‘ছেড়ে আসা গ্রাম’-এর অশ্রুসজল কাহিনিমালার জন্ম। কাহিনিগুলি বিভিন্ন সূত্র থেকে, অনেক শিবিরবাসী মানুষের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য নিয়ে রচিত। তাই কোথাও কোথাও এতে অসম্পূর্ণতা ও তথ্যঘটিত অসংলগ্নতা থাকা স্বাভাবিক। তা ছাড়া সেই অভাবনীয় রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের কালে অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন গ্রামের কাহিনি নিখুঁতভাবে সংগ্রহ করাও সহজ ছিল না। তবু আপন আপন গ্রাম-পরিচয় দিয়ে আমার যেসব সহকর্মী ও অপরিচিত বহুজন আমার এই পরিকল্পনা রূপায়ণে সাহায্য করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের কাছে আমার কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। কাহিনিগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের অনুমতি দেওয়ায় আমি যুগান্তর-কতৃপক্ষের কাছেও বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।
ছেড়ে আসা গ্রাম-এর প্রথম খন্ড প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৬০ সনের পুণ্য পঁচিশে বৈশাখ তারিখে। তাতে কেবলমাত্র ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল (বাখরগঞ্জ) ও ময়মনসিংহ জেলার কয়েকটি করে গ্রাম-চিত্র প্রকাশ করা হয়েছিল। তখন থেকেই বহু অনুরোধ ও তাগিদের পর তাগিদ আসতে থাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত তখনকার পূর্ববাংলার অন্যান্য জেলার গ্রাম পরিচয়ও গ্রন্থাকারে মুদ্রণের জন্যে। নানা কারণে, বিশেষ করে কোনো কোনো জেলার (বিশেষত পাকিস্তানভুক্ত উত্তরবঙ্গের) গ্রাম-তথ্য সংগ্রহে বিলম্ব হওয়ায় ছেড়ে আসা গ্রাম গ্রন্থের দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশে বেশ দেরি হয়ে যায় এবং তা ছাপা হয় পাঁচ বছর পরের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে। এই খন্ডে ছিল চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, যশোহর, কুষ্টিয়া, খুলনা, রাজসাহী, পাবনা, মালদহ, রংপুর, বগুড়া, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি জেলার পল্লিচিত্র। পূর্ব ও উত্তর বাংলার এসব স্নিগ্ধ, শ্যামল গ্রামের অশ্রুসজল বর্ণনায় একই বেদনা-মধুর সুর প্রত্যেকটিতে ধ্বনিত হলেও বিভিন্ন জেলার লোকাঁচার ও লোকসংস্কৃতির পরিচয় সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে বিভিন্ন কাহিনিতে।
বলে রাখা ভালো, এই গ্রন্থের কথাচিত্রগুলি ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রচিত নয়। সাধারণ গ্রামীণ মানুষের স্বপ্ন-প্রেরণা, স্নেহলালিত চেতনা ও সুখ-দুঃখ-মধুর স্মৃতি-চিন্তা প্রত্যেকটি বিবরণকে আবেগাপ্লুত করে তুলেছে। বস্তুত মানুষই এখানে মূলকেন্দ্র, বাস্তুত্যাগী মানুষের বিহ্বল চেতনাকে কেন্দ্র করে রচিত এক-একটি বর্ণনায় এক-একটি ছেড়ে আসা গ্রাম হয়ে উঠেছে জীবন্ত। তথাপি ইতিহাস এখানে অপ্রত্যক্ষ হলেও ভবিষ্যতের মানুষকে কোনো কোনো ঐতিহাসিক সূত্রের সন্ধান দানে এই গ্রন্থে গ্রথিত গ্রাম-চিত্রগুলি হয়তো সাহায্য করবে।
দেশবিভাগের পর থেকে বছরের মধ্যে ছেড়ে আসা গ্রাম-এর প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড প্রকাশের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তৎকালীন পাকিস্তান সরকার এ দু-খন্ড বইকে সে-দেশে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করে। ফলে, চাহিদা থাকতেও পূর্ববঙ্গে সে-সময়ে এ বই যেতে পারে না। তবু উভয় খন্ডই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে-পড়া উদবাস্তু বাঙালিদের চাহিদায় অল্প কিছুদিনের মধ্যে নিঃশেষিত হয়ে যায়। তারপর পাকিস্তানের কবল থেকে মুক্ত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে গিয়ে সেদিন ও এদিনের পরিপ্রেক্ষিতে নিজ নিজ পিতৃপুরুষের ভিটে বা জন্মগ্রামকে মিলিয়ে দেখবার বাসনায় ছেড়ে আসা গ্রাম গ্রন্থ ক্রয়ে উদগ্রীব হয়ে ওঠেন ছিন্নমূল বাঙালিরা এবং স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিকরাও এই গ্রন্থখানি পাওয়ার জন্যে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন। সবারই ইচ্ছে, একখন্ডেই গ্রন্থটি প্রকাশিত হোক। বহু বাঙালি পাঠকের সেই আগ্রহ-পূরণে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা’-কতৃপক্ষ যে-সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান এই দলিল-গ্রন্থখানি প্রকাশ করতে পারলেন, সেজন্যে তাঁদের আন্তরিক প্রয়াস সত্যি প্রশংসাহ। পাঠকগণ এই গ্রন্থের প্রতিটি কাহিনির অন্তরালবর্তী ভাগ্যবিড়ম্বিত ছিন্নমূল বাঙালির বেদনার্ত অন্তরের স্পর্শ অনুভব করতে পারবেন, আশা করি।
দক্ষিণারঞ্জন বসু
বড়োদিন
১৩৮২
.
সূচিপত্র
ঢাকা জেলা – বজ্রযোগিনী সাভার ধামরাই খেরুপাড়া ধামগড় আনরাবাদ শুভাঢ্যা নটাখোলা সোনারং
ময়মনসিংহ জেলা – নেত্রকোণা বিন্যাফৈর কমলপুর খালিয়াজুরি বারোঘর কালীহাতী সাঁকরাইল নাগেরগাতী সাখুয়া
বরিশাল জেলা – বাণারিপাড়া গাভা কাঁচাবালিয়া মাহিলাড়া চাঁদসী সৈওর নলচিড়া
ফরিদপুর জেলা – কোটালিপাড়া রামভদ্রপুর কাইচাল খালিয়া চৌদ্দরশি খাসকান্দি কুলপদ্দি
চট্টগ্রাম – সারোয়ালি ধলঘাট ভাটিকাইন গোমদন্ডী
নোয়াখালি – দরাপনগর সন্দীপ
ত্রিপুরা – বায়নগর চান্দিসকরা বালিয়া কালীকচ্ছ।
শ্রীহট্ট – পঞ্চখন্ড রামচন্দ্রপুর
যশোহর – অমৃতবাজার সিঙ্গিয়া
খুলনা – সেনহাটী শ্রীপুর ডাকাতিয়া
রাজসাহী – হাজরা নাটোর তালন্দ বীরকুৎসা
পাবনা জেলা – গাড়াদহ পঞ্চকোশী ঘাটাবাড়ি সাহজাদপুর
কুষ্টিয়া – শিলাইদহ ভেড়ামারা
মালদহ – কালোপুর
রংপুর – হরিদেবপুর
বগুড়া – ভবানীপুর
দিনাজপুর – ফুলবাড়ি রাজারামপুর
জলপাইগুড়ি – বোদা
মালদহ – কালোপুর
গম্ভীরার আসর বসেছে গ্রামে। ওস্তাদ পরাণ মাঝি সুললিত কণ্ঠে গাইছে, ‘শিব হে, এবার পূজা বুঝি তোমার হইল না। অনেকদিন শুনেছি এই গান, প্রতিবারই শুনেছি। কিন্তু কোনোদিন কি ভেবেছি এমন একদিন আসবে যেদিন সত্যিই শিবের পুজো আর হবে না গ্রামে।
ভীতস্ত আশঙ্কাম্লান একদল লোকের মিছিল চলেছে গ্রাম থেকে বাইরে, কোথায় কেউ জানে না। একা তাদের পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল দোস্ত মহম্মদ–জোয়ান লাঠিয়াল দোস্ত মহম্মদ। বলেছিল, ‘কুণ্ঠে যাবে, যে যাবে তার মাথা লিয়ে লিব। তাকেও পথ ছাড়তে হল। লাঠি ফেলে দিয়ে কেঁদে উঠল দোস্ত মহম্মদ। মালদহ জেলার অখ্যাত কালোপুরে ইতিহাসে আর-একটি নতুন অধ্যায় শুরু হল। দোস্ত মহম্মদ কাঁদছে, দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল দোস্ত মহম্মদ কাঁদছে! কেন? এ প্রশ্নের জবাব নেই। ওপরে নির্বাক আকাশ। পায়ের নীচে পাতাজড়ানো তামাটে রঙের পথ কথা কয় না।
উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলার ছোটো একটি গ্রাম কালোপুর। গ্রাম নয়, যেন একটি দ্বীপ। সভ্যজগতের কলকোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন শান্তিপ্রিয় আত্মসুখী জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত সে দ্বীপ। ছোটো ছোটো মানুষ ছোটো ছোটো তাদের আশা-আনন্দ, সুখ-দুখ। প্রাচীন গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ আজও যেখানে দেখা যায়, সেখান থেকে খুব দূরে নয়, মাইল দশেকের মধ্যেই। কিন্তু কী সেকালে, কী ইংরেজ আমলে, ইতিহাসের ওঠাপড়ায়, রাজা-উজিরের আসা-যাওয়ায় কেমন একটা অপরিবর্তনীয়তা গ্রামটিকে পেয়ে বসেছিল! হঠাৎ এল আঘাত-অপ্রত্যাশিত, অভাবিত। বিমূঢ় মানুষগুলো একান্তই গেয়ো, বুঝেই উঠতে পারেনি কত বড়ো ঝড় তাদের আম-জামের ছায়ায় ঘেরা ঘরগুলোর ওপর নেমে এল। সর্বনাশ যখন এল, তখন তারা বুঝল কী তাদের ছিল, কী তারা হারাল।
মালদহ জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের শিবগঞ্জ থানার এলাকায় পড়ে গ্রামটি। আমবাগানের ঘনবিস্তৃত ছায়ায় এলোমোলা ঘরগুলো। খড়ের চালা, মাটির দেওয়াল। ছোট্ট একটুকরো উঠোন। এ গাঁয়ে যাদের বাস–চাষ-আবাদ করেই চলে তাদের জীবিকা। এরা সকলেই প্রায় মুসলমান।
গাঁয়ের দক্ষিণে কয়েক ঘর হিন্দুর বাস। তাদের কেউ কামার, কেউ কুমোর, কেউ তাঁতি। কৈবর্ত আর তাঁতিদের সংখ্যাই বেশি। কেউ কেউ জাতব্যাবসা করে বটে, কিন্তু চাষ সবাইকেই করতে হয়–না হলে চলে না। আমাদের বাড়িটা একেবারে মুসলমান পাড়ায়। ডাইনে-বাঁয়ে তাদের ঘর। সামনে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ধুলোটে রাস্তা। ভোরবেলা থেকেই গোরুর গাড়ির চাকার শব্দে ঘুম ভাঙত গ্রামের। ভিনগাঁয়ের লোকেরা আসা-যাওয়ার পথে এই ছোট্ট গাঁয়ের দিকে কেউ-বা তাকাত–কেউ-বা তাকাত না।
গাঁয়ের পাশ দিয়ে চলে গেছে গঙ্গা নদী। অপ্রশস্ত শীর্ণ। শীতের সময় চর পড়ে–বর্ষায় থইথই করে। উত্তর বাংলার অন্য সব গ্রামের মতোই কালোপুরেও নেই ষড়ঋতুর বিপুল ঐশ্বর্য। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের আভরণহীন প্রকৃতি ক্ষতিপূরণ করে আম-জাম দিয়ে। তারপর বর্ষা। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ধুলোভরা রাস্তা কর্দমাক্ত হয়ে যায়, নীচু জমির জল উপচে ওঠে। কিন্তু তবু গোরুর গাড়িই প্রধান বাহন–নৌকো নয়। নৌকো যা চলে তা গঙ্গায়। বড়ো বড়ো পালতোলা নৌকোগুলো এ গাঁয়ের কাছে ক্কচিৎ নোঙর ফেলে। বর্ষা এ গাঁয়ে আসে অভিসম্পাতের মতো, পুরোনো খড় চুঁইয়ে ঘরে জল ঝরে। বর্ষার পর শরৎ। কত নাম-না জানা ফুল ফোটে–ঝোঁপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে মিঠে রোদ উঁকি মারে। কিন্তু এ সময় প্রকৃতি তার ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেয়। পুজোর আনন্দের হাসি মিলিয়ে যেতে না যেতেই ম্যালেরিয়া দেখা দেয়। হেমন্ত আর শীত কেটে গেলে পর ম্যালেরিয়ার মেঘও কেটে যায়। বসন্তই এ গ্রামে সত্যিকারের ঋতু। আমের পাতায় নতুন রং ধরে–গাছে গাছে থোকা থোকা মুকুলের গন্ধে গ্রাম-পথ মেতে ওঠে। জানা-অজানা পাখির ডাকে গ্রামের আকাশ মুখর। সে কী আকর্ষণ!
কিন্তু আজ সে গ্রাম দূরে–অনেক দূরে। পরিচিত মুখগুলো মনে পড়ে–পরিচিত মাঠ, নদী, বাগান, খেত এমনকী গাঁয়ের সেই খোঁড়া কুকুরটাকে পর্যন্ত। আর আমাদের চন্ডীমন্ডপ। স্বল্পবিত্ত মুসলমান চাষি আদালতে যেত না, এই চন্ডীমন্ডপেই ভিড় জমাত বিচারের জন্যে। বাড়ির কর্তাকে এরা সবাই বলত ঠাকুরমশাই। এমনকী শিবগঞ্জ, কানসাট, মোহদিপুকুর, দেওয়ানজাগীর লোকেরাও চিনত তাঁকে। গাঁয়ের যেকোনো বিবাদ মেটাতে, আনন্দে উৎসবে আর দুঃখের দিনে–সব সময়ই তিনি থাকতেন গাঁয়ের লোকের পাশাপাশি। আর এই চন্ডীমন্ডপ ছিল গাঁয়ের আদালত।
বছরে গ্রামে একবার করে রটন্তী কালীপুজো হত। সে পুজো হয় মাঘ মাসে। তাতে হিন্দু মুসলমান সবাই যোগ দিত। মুসলমান চাষিদের কাছেও এ সময়টা যেন পরবের।
সারারাত জেগে তারা আলকাপ আর গম্ভীরা গাইত।
গম্ভীরার নাচের তালে তালে উদ্ভাসিত হয়ে উঠত সারাগ্রাম। নানারকম গালগল্প অবলম্বন করে যে গান হয় তাকেই এদেশের লোক ‘আলকাপ’ বলে। দু-পক্ষের বক্তব্য বিনিময় গানের মাধ্যমে। নাট্যরসও থাকে তাতে। হাস্যরসেই এর পরিণতি। বিধবা বিবাহ নিয়ে আলকাপ ব্যঙ্গ গানের একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাক। কন্যাদায়গ্রস্ত স্বামী স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়ে বলছে,
আমার কথা শুনেক বামনী চুপ কর্যা থাক… (টে)
জামাই আনব গাড়ি গাড়ি লাখে-লাখ…(টে)
উত্তরে স্ত্রী বলছে,
ঘরে রাখ্যা কুমারী, উদ্ধার করছ কুড়্যার আড়ি–
মাথাতে জ্বালিয়া তুষের আগুন,
বাহিরে বেড়াইছ পটকা চাল্যা–
অর্থাৎ ঘরে কুমারী মেয়ে, মাথায় তুষের আগুন জ্বলছে, আর তুমি কিনা বিধবা উদ্ধার করার চাল মেরে বেড়াচ্ছ। গানগুলো হয়তো অনেকাংশেই স্থূল আর গ্রাম্য–কিন্তু তবু বাংলার লোকসংস্কৃতির ইতিহাসে এই সব বিলুপ্তপ্রায় আলকাপ আর গম্ভীরা একেবারে মূল্যহীন নয়। সেটেলমেন্টের অফিসারকে দেখে গ্রাম্যলোকের ব্যস্ততা, ভয় আর কিছুটা বিদ্বেষের ছবি কি ফুটে ওঠেনি এই গম্ভীরা গানে?
এ দাদু আয়না দৌড়া চট করা,
এ শালার এমন জরিপ এমন তারিখ
মারল মুলুক জুড়্যা।
আমিন বাবু চেনম্যান লইয়া
ঝনমন করা আইসছে,–
খেত-আলার গড় দেখ্যা র্যাগ্যা
যে লাল হইচ্ছে।
এসব গান এদের মুখে না শুনলে বোঝাই যায় না, তীক্ষ্ণ বিপকে কী করে এরা হাস্যরসে রূপান্তরিত করতে পারে। দেশের মুক্তি আন্দোলনে উদ্দীপনাদানে এবং দেশবাসীর ওপর পাশ্চাত্য শিক্ষার কুপ্রভাবের কঠোর সমালোচনায় গম্ভীরা গানের মুখরতা অবিস্মরণীয়। পল্লিকবি মহম্মদ সুফির রচিত একটি গম্ভীরা গানের নিম্ন পঙক্তি কয়টিতে কী আন্তরিক জ্বালাই না ফুটে উঠেছে! কবি লিখছেন—
(আমরা) বিলাসিতায় বাংলাকে হায়
মাটি করলাম ভাই রে!
(আমরা) ছিলাম বা কী, হলাম বা কী
বাকি কিছুই নাই রে!
(আমরা) দু-পাতা ইংরেজি পড়ে
কৃষি-শিল্প তুচ্ছ করে,
বাপ-দাদাদের ব্যাবসা ছেড়ে–
(পরের) মুখপানে চাই রে!
এসব গান আজ মনে পড়ে–আর গ্রামের ছোটো-বড়ো কত ঘটনাই না সারামনকে ঘিরে ধরে। মনে পড়েছে জহর আলি কাকার কথা। আমাদের বাড়িতে একবার চুরি হয়েছিল। সবাই সন্দেহ করল জহর আলিকে। তিনি তো কেঁদেই অস্থির। তিনি যে নির্দোষ!
আলি কাকা চমৎকার গল্প বলতেন। তাঁর ছেলেবেলায় তাঁর মুখে শোনা গৌড়ের জিনের কাহিনি আজও ভুলিনি। গভীর রাতে গৌড়ের পথ ধরে চলেছে গোরুর গাড়ি। গাড়োয়ান গাইছিল কী একটা গান। হঠাৎ থেমে যেতেই অশরীরী জিন পেছন থেকে শুনতে চাইল পরের লাইন। তারপর কী হল বলতে গিয়ে জহর আলি কাকা গাড়োয়ানের সৌভাগ্যের যে চিত্র এঁকেছিলেন তা ভোলবার নয়।
আর দোস্ত মহম্মদ। ফর্সা জোয়ান ছেলে। কখনো আমাদের জমিতে গোরু-বলদ নামিয়ে ধান খাইয়ে দিত, কখনো আখের জমিতে লুকিয়ে আখ খেয়ে যেত। আমরা গ্রাম ছেড়ে চলে যাব শুনে মস্তবড়ো বাঁশের লাঠি আঙিনায় ঠুকতে ঠুকতে চিৎকার করে বলতে লাগল–কুষ্ঠে যাবে, যে যাবে তার মাথা লিয়ে লিব। ভয়ে বাড়ির সবার মুখ শুকিয়ে এল। দাদা বেরিয়ে এসে হাসতে হাসতে বললেন- কী মহম্মদ তুমি, তুমি আমাদের মারবে?
মহম্মদ চোখ তুলে তাকাতেই পারল না। বাঁশের লাঠিটা ফেলে দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে চলে গেল। যেদিন গ্রাম ছেড়ে চলে আসি সেদিন তার সে কী কান্না! আশ্চর্য ছেলে।
গাঁ থেকে মাইল খানেক দূরে শিবগঞ্জ থানা এলাকা–সেখানেই পোস্ট অফিস, ইউনিয়ন বোর্ড, স্কুল সব কিছু। আমাদের কালোপুর গ্রামের চোখে প্রায়-শহর সেটি। সেখান থেকেই প্রথম দাঙ্গার খবর এল। মুসলমান চাষিরা আমাদের যেতে দিতে চায়নি। কিন্তু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের রাখতে ওরাও আর সাহস পেল না।
সেই গ্রাম আজও কি তেমনি আলকাপের দিনে মেতে ওঠে? গম্ভীরায় আজও কি তেমনি হিন্দু-মুসলমান একযোগে চিৎকার করে গান ধরে- ‘শিব হে, এবার পূজা বুঝি তোমার হইল না, হইল না? ধান উঠলে কি তেমনি হাসে– অনাবৃষ্টি হলে তেমনি কাঁদে।
এদের ছেড়ে আসতে ভারি কষ্ট! আমাদের আসার পথে এদের চোখে যে জল দেখেছি তা কী করে ভুলব। আজ আর সে গাঁয়ে ফেরার পথ নেই। ধান উঠুক, জহর আলির জিন আমাদের ডাকুক, দোস্ত মহম্মদ কাঁদুক, তবু, সেই ‘ছেড়ে আসা গ্রাম থেকে আমরা অনেক দূরেই পড়ে থাকব!
ময়মনসিংহ জেলা – নেত্রকোণা বিন্যাফৈর কমলপুর খালিয়াজুরি বারোঘর কালীহাতী সাঁকরাইল নাগেরগাতী সাখুয়া
বর্ষণের আর বিরাম নেই। গায়ে কাপড় চাপা দিয়ে শুনি বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, টিনের ছাদের ওপর ঝম ঝম জল ঝরছে। রাত সাড়ে আটটায় পথঘাট নিশুতি, কারও সাড়া শব্দ নেই। হ্যারিকেনের আলোয় খাটের কোনায় মা বসে উলের প্যাটার্ন তুলছেন। বাড়ির পেছন দিয়ে অন্ধকার বৃষ্টিভরা রাতে সাড়ে আটটার ট্রেন শিস দিয়ে গেল। পাশেই কোর্ট স্টেশনে একটুকরো কোলাহল জেগে আবার মিলিয়ে গেল। সেই বারিবর্ষণের কিন্তু তবু বিরতি নেই!
গারো পাহাড়ের তলায় আমার পাহাড়তলির শহর, মগরা নদীর পাকে পাকে জড়ানো। সারাবছরে আট মাস তার বর্ষার সঙ্গে মিতালি। যখন মগরায় ঢল নামে, মানুষের হাঁস ভাসিয়ে নিয়ে যায়। মাঝে মাঝে ঘরবাড়ি ভেসে আসে, দু-একটা ছাগল গোরুও আসে। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ে, জলের ওপর ফুটকি ওঠে। কালীবাড়ির ঘাটে জল তোলপাড় করে ঝাঁপাই সাঁতরাই। বাংলার উত্তর-পূর্বতম প্রান্তে লাল সুরকির পথে যেখানে দাঁড়ালে গারো পাহাড়ের নীলাঞ্জন রেখা সবুজ হয়ে দেখা দেয় সেইখানে পাখপাখালি আর ফলন্ত ফসলের দেশে আমার ছোট্ট মহকুমা শহর, নেত্রকোণা। মেঠো পথ ভেঙে পাহাড়ি আনারস, কমলালেবু, আর চাল নিয়ে যে গাঁয়ের মানুষেরা আসে শনি-মঙ্গলের হাটে তারা বলে, কালীগঞ্জের শহর। নদীর ঘাটে পাটের বোঝা খালি করে দিয়ে রাত্রে নৌকোর মাঝিরা ভাটির দেশের গান গায়। অন্ধকারে জোনাকির তারার মতো ওদের কেরোসিনের পিদিম জ্বলে–ওরা বলে ‘কুপি’। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ওদের ‘ব্যাপারী নাও’-এর কাজ-কারবার কত দেখেছি। ওরা আরও ভাটির দেশের গল্প শোনাত, যেখানে আরও জল, আরও ধান আর ‘উড়া হাঁস’। রাত্রে সেই জলের মধ্যে ‘জিনের বাতি জ্বলে, তখন পিরের নাম স্মরণ করতে হয়, পাঁচ আনার সিন্নি মানতে হয়। না হলে ওই জিনের ‘ভুলা বাতি’ ঘুরিয়ে মারে, চোখে দিশা লাগে। আমাদের এই দেশে বর্ষার প্রকোপটা কিছু যখন কমে, আকাশের বর্ষণ থামে আর মাঠে-ঘাটে যখন জল কলকল করে ছোটে তখন পাহাড় ডিঙিয়ে দূর দেশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বুনো হাঁস আকাশে ছায়া ফেলে আসে। গাঁয়ের মানুষ বলে, ‘উড়া হাঁস’।
তাই যদিও আমাদের ওই শহরে তিনটে ছেলে আর একটা মেয়ে-ইস্কুল আছে, আদালত কাছারি আর দু-দুটো ছোটো রেল স্টেশন আছে–যদিও মিটার গেজ লাইনে দিনে দু-বার আসা যাওয়ার ট্রেনে মাছ আর পাট চালান যায়, তবু নেত্রকোণা শহর হয়ে উঠতে পারেনি।
চেষ্টার অন্ত ছিল না। কে কে সেনের মতো জবরদস্ত আই. সি. এস. অনেক মহৎ উন্নয়ন আন্দোলন করলেন, কিন্তু নেত্রকোণার মানুষের গেঁয়োমি কাটল না। মহকুমা হাকিম বৈদ্যনাথন যেদিন শহরের রাস্তায় প্রথম প্রচন্ড লাল ধুলো উড়িয়ে মোটর চালালেন সেদিন বড়োদের আর বিরক্তির সীমা ছিল না। শহরের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সেদিন উকিল মহলে ঘোরতর দুশ্চিন্তার কারণ ঘটেছিল। অতঃপর এমনতর দুর্বিপাক আর শহরের ধার ঘেঁষতে পারেনি।
এখানকার মানুষের নিত্যদিন চর্চায় দশটা-পাঁচটার বন্ধন ছিল নগণ্য–তার ভারবাহী ছিল অসহায় ছাত্ৰকুল আর আমমোক্তার মুহুরি-উকিলবাহিনী। আদালত আর ফৌজদারি এজলাসে দিন ছিল অফিসি ঢঙ-এ বাঁধা। আর কোনো অফিস-কাছারির স্থান তখন নেত্রকোণায় ছিল না। যুদ্ধ-দেবতার সন্তান হিসেবে সাপ্লাই আর কন্ট্রোল এবং আরও এবম্বিধ অফিস যখন পক্ষ বিস্তার করল, সে অনেক পরের কথা। সেই নগণ্য সংখ্যকের বাইরে আমরা ছিলাম ভোরবেলা ফেন-ভাত-খাওয়া মানুষ, দ্বিপ্রহরের ভোজনপর্ব সমাধা করতে দেড়টার ট্রেন এসে পড়ত, শুরু হত সায়াহ্নের প্রারম্ভকাল। আহার্যের প্রাচুর্যে যেমন অনটন ছিল না, সময়ের বিস্তৃতিকে সুখের আড্ডায় রসিয়ে তোলারও তেমনি কৃপণতার প্রয়োজন হয়নি। ছোটোবেলায় ইস্কুল যাতায়াতের পথে দেখতাম তেরিবাজারের তেমাথায় অভয়দার চায়ের দোকানে বয়স্ক মহলের ভিড়। সাদা পিরিনে সোনালি পানীয় চা-এর সঙ্গে আমাদের তখনও আলাপ হয়নি। সেখানে কখনো কখনো বৃষ্টি পড়তে আশ্রয় নিয়েছি, দেখতাম নুয়ে-পড়া ঘরের আবছায়া কোণে একদিকে কেটলি ধূমায়মান, অন্যদিকে অভয়দার প্রশস্ত তক্তপোশে গুটিসুটি বসে বারোইয়ারি আলাপে মত্ত বয়োজ্যেষ্ঠ দল। তাঁদের আলোচনার অর্থ বুঝতাম না। কিন্তু তখনই, নেত্রকোণার ছেলে আমরা, বুঝতে শিখেছি যে, এ-রসের তুলনা নেই। যে কহে আর যে শোনে সবাই পুণ্যবান। এঁরা কেউ অভয়দার কাঁথা টেনে, কেউ সিগারেট ধরিয়ে বসেছেন বর্ষার প্রায়ান্ধকার সন্ধ্যায়, নিম্নস্বর গুজব-আলাপনে। ঘর গুলজার। এই অভয়দার চায়ের দোকানের সামনে ছিল আমগাছ একটি, তাতে কদাপি ফল ধরেছে। আমের নামে না থোক, আমতলা ছিল অন্য কারণে শহরের সকল জীবনের কেন্দ্রস্থল। এই অভয়দার ঘরের ভেতরে শীতের রাত্রি আর বর্ষায়, গ্রীষ্মে ও শরতে সম্মুখবর্তী আমতলায় বিশ্ব-রাজনীতি ও ঘরোয়া নীতি নিয়ে নানা আলোচনা হয়েছে। পরবর্তী বয়সে আমরা আমতলা আর অভয়দার দোকানের উত্তরাধিকার পেয়েছিলাম। কিন্তু তারও পূর্বে আড্ডার অমৃত সুখ আমরা উপভোগ করেছি। কালীবাড়ির দো-মাথার কাছে আমাদের বাড়ির পশ্চিমে রাস্তার পাশেই কাঁঠাল গাছের ছায়ায় ছিল সুখলালের বাঁশের মাচা। আমরা বলতাম,–সুখলালের চাঙাড়ি। সেইখানে নিত্য সকালে আমাদেরও আসর জমত, প্রথম প্রথম সুখলাল তাড়া করত। অবশেষে সেখানে আমাদের অধিকার পাকা হল। সামনের দোকানে পোদ্দার মশাই হাতুড়ি ঠুকতেন, তাঁর ঘর নদীর ঢালু পাড়ে কাত হয়ে পড়েছে। তাঁর ছেলে শ্রীমান রামু ছিল আমাদেরই শাগরেদ। কী যে কথার ভান্ডার ছিল জানি নে, কিন্তু ছুটির দিনে আমাদেরও সেই বেলা একটা। সেখানে খেলার মাঠের দল পাকানো, কাঁচা আম ও লিচু চুরির জল্পনা, সুধীর মুজমদারের গোঁফ, এমনকী যুগান্তরের দাদাদের সেই সব রোমাঞ্চকর আগ্নেয় অভিযানের বিষয়ও ছিল আলোচ্য বস্তুর তালিকায়। রাজনীতি ক্ষেত্রে তখনই আমাদের মতো দশ-বারো বৎসরের অবোধদের প্রবেশাধিকার মিলেছে। সুধীর মজুমদার মশাই হিজলি না বক্সার কোন জেল থেকে সাত-আট বৎসরের সাধনায় বিরাট এবং সামরিক ধরনের একটা গোঁফ নিয়ে ফিরেছেন। তাঁর নেতৃত্বের আর বাধা রইল না। পাড়া জুড়ে সাড়া পড়ল। সাজ, সাজ, সাজ। তখন পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গ দর্শনের সৌভাগ্য প্রায় কারুরই হয়নি। কিন্তু হলে কী হবে, নেতাজি সুভাষচন্দ্র হঠাৎ কোথা থেকে একবার এসে পড়লেন, শহরে সে কী হইহই কান্ড! তখন জানা গেল শ্বেতাঙ্গ নামক একদল রক্তপায়ী পশু সত্যই দেশে আছে। আমার কাকু এবং পাড়ার গণেশদা বিপ্লবীদের দু-একটা সত্যি কাহিনি আমাদের শোনাতে শুরু করেছেন। কোথাও কোনো অপরাধ করলে কিংবা লুকিয়ে পান খেলে অথবা তাস খেললে তাঁদের কাছে বকুনি ও উপদেশের সীমা থাকত না। বাড়ির অভিভাবকেরাও তখন ছেলেদের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে পাড়ার দাদা তথা রাজনীতির দাদাদের কাছেই নালিশ জানাতেন। সব মিলে আমাদের ছোটো শহরের তিনটি জিনিস ওই বয়সেই প্রধান হয়ে উঠল–আচ্ছা, পাড়া ও রাজনীতি। পাড়ার দাদারা ছিলেন বাড়ির এবং রাজনীতি ক্ষেত্রের অভিভাবক। কিছুদিন পরে আরও আট-দশজন দাদা কারাবন্ধন ঘুচিয়ে বেরিয়ে এলেন–দেখতে দেখতে আমতলার আড্ডা গরম হয়ে উঠল! আমাদের ইস্কুল যাওয়ার পথের পাশে তেরিবাজার ও মেছুয়াবাজারের মাঝামাঝি জায়গায় একটা কংগ্রেসের কার্যালয়ও জেঁকে উঠল। কালীবাড়ির নাটমন্দিরে মেয়েদের একটা সভা ডেকে কীসব প্রস্তাব গৃহীত হয়ে গেল। সে সময়ে লাল সুরকির পথের পাশে একদিকে ছিল নদী, অন্য দিকে একসারি বাড়ি, তার পেছনে ধানখেত। আমাদের শহরটা একপ্রস্থ বাড়ি ছাড়িয়ে আর ঘনত্বে বাড়ল না, কেবলই বিস্তৃত হয়ে চলেছিল! এই বাড়িগুলোর পেছন দিকে ছিল আর একটা শানপাতা ছোটো পথ, ধানখেতের পাশ দিয়ে। সে পথটা মহিলাদের অন্তঃপুর থেকে অন্তঃপুরে গতায়াতের যোগসূত্র। ধীরে ধীরে সে পথ ছেড়ে মহিলারা ক্রমশ বেরোলেন সামনের সদর রাস্তায়।
এতকাল দেখেছি মেয়ে-ইস্কুলের ‘ঝি’ এসে বেলা ন-টায় একবার রাস্তা দিয়ে হাঁক পেড়ে যেত। তারপর খালি পা, ভেজা চুল, গাছকোমর-শাড়ি একপাল মেয়ে তাড়িয়ে সেই ‘ঝি’ তার ছাতা ও ছেঁড়া চটি টানতে টানতে মোক্তারপাড়ার দিকে পথ ধরত। সেখানে দুই মানুষ উঁচু টিনের বেষ্টনী তুলে মেয়ে-ইস্কুল স্তব্ধ। আর তারই উলটো দিকে দত্ত হাই-এর দিলদরিয়া খোলা মাঠে আমাদের দিনভর হইহই। বছরে একটি দিন সন্ধেবেলায় সেই মেয়ে-ইস্কুলের টিনের দরজা খুলত, ছেলে-মেয়েতে মিলে সেদিন হত রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব। দাদাদের কাছে শুনতাম, শান্তিনিকেতনের বাইরে রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব প্রথম হয়েছিল আমাদের এই পান্ডববর্জিত দেশে। কিন্তু ধীরে ধীরে সেসব দিন সরে গেল। এখন ঝি ছাড়াই মেয়েরা চলেন, দু-একটা বিদগ্ধ রাজনীতি আলোচনায়ও ওঁদের অঞ্চলের ছায়াপাত ঘটে। দিন কাটছিল বেশ। শহর জুড়ে রাজনীতি ছাড়া কথা নেই, দেখতে দেখতে আরও চায়ের দোকান বসল তেরিবাজারের পাড়ায়। নদীর ঢালু পাড়ের ওপর তাদের ঝোলানো বারান্দা, বর্ষায় জল এসে নীচে খেলা করে। যুবা, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধের জন্যে বয়ঃক্রমে নির্দিষ্ট হল চায়ের ঘর-তারও মধ্যে কংগ্রেস, আর. সি. পি. আই. ও কম্যুনিস্টদের চা-পান সভা পৃথক হল। আমতলা থেকে শুরু করে নদীর ধারে ধারে পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়ল রাজনৈতিক দলের আলাপন গৃহ। মাঝখানে অভয়দা আর মানিকের ঘরে চায়ের আড্ডা সর্বজনের। সকল দলের লোক সেখানে আসে। চেঁচিয়ে পাড়া গরম করে তারপর ধীরে সুস্থে নিজের নিজের চা-ঘাঁটির বিবরে গিয়ে ঢোকে। এইসব চায়ের দোকানে একটা কাল্পনিক বিদগ্ধতার ভাব ছিল প্রখর। বড়ো বড়ো লিখিয়েদের নাম শোনা যেত প্রায়শই। তার মধ্যে বিদগ্ধতায় অগ্রণী তরুণ সভাগুলো, সেখানে যোশী, এম. এন. রায়দের উক্তি নিয়ে তক্তপোশ ফাটে। ভাবী সংগ্রামের নীতি ও পথ এবং জার্মান জাতির কখনো রণবল ও ইয়োরোপের ভবিষ্যৎ আলোচনায় কখনো হাতাহাতিরও জোগাড় হত কসমোপলিটান ঘর অভয়দা ও মানিকের দোকানে। তবে তার মধ্যে হঠাৎ হালকা হাওয়ার মতো সলিলদার হাসির কথা ছুটত, বিমলদার রবীন্দ্রগীতির ভান্ডারও ছিল অফুরান। ঠাণ্ডা হতে সময় লাগত না। এই ছোটো শহরে যেমন আট বছরের ছেলেও দল করে, তেমনি কেউ আবার দলাদলিতে নেই। সমস্ত কিছুরই ওপরে আড্ডা আর হো হো করে দিন কাটিয়ে দেবার এমন একটা নেশা ছিল যে, কারুরই নিষ্ঠা সহকারে ঝগড়া করার সময় মিলত না। কম্যুনিস্ট পার্টির যিনি প্রধান দাদা ছিলেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের ছেলেরাও ঝুলে থাকত। কোনো একটা অন্যায় আচরণের জন্যে আর, এস, পি-র ছেলেকে ডেকে ধমকে দিতেন কংগ্রেসের মুখ্য নেতা। আড্ডার ঘড়ি চলেছে সকাল আটটা থেকে বেলা একটা, তারপর কয়েক ঘণ্টার বিরতি দিয়ে আবার রাত সাড়ে আটটা অবধি। তারও পরে রাত্রির খাওয়া সেরে, বাছাই করা কয়েকটি দলনির্বিশেষে গোষ্ঠী আছে, তাদের আসর জমে নদীর পারে ঘাটলায় ঘাটলায়। কালীবাড়ির ঘাটে আমাদের আসন ছিল নির্দিষ্ট করা। শচীবাবুর বাড়িতে সান্ধ্য আসর জমত সাহিত্য ও সংগীতের। সে বাড়ির মেয়েরা ছিলেন রুচিতা। কলেজ ছুটির অবসরে তাঁদের হত দুষ্প্রাপ্য আবির্ভাব, কিন্তু তবু সুখলভ্য। অনেকদিন আমার পড়ার ঘরটিতে নির্বাচিতদের শুভাগমনে সন্ধ্যা জমে উঠত, বারিবর্ষণ তাকে আরও নিবিড় করত। হয়তো গানের সুর শুনে তেরিবাজারের আড্ডা-শেষের দু-একজন গৃহমুখী পথ ছেড়ে আস্তে এসে আসন নিত। বীরেন্দ্রকিশোরের পৃষ্ঠপোষিত উচ্চাঙ্গের মিউজিক কনফারেন্স ও রবীন্দ্র জয়ন্তী এক দিকে, অন্য দিকে রাজনীতি, অফুরন্ত সময় আর আড্ডা–এই গৌরবে গৌরবান্বিত নেত্রকোণা। এখানকার যুবকেরা বিদ্যার্জনের জন্যে যদি বা যায় বাইরে, বিদ্যাবিক্রয়ের জন্যে নয়। লোকে বলে সকালবেলায় ফেনভাত আর আড্ডার টান,–যাক জগৎ উচ্ছন্নে! থাকুক শুধু এককলি গান, দুটি রাজনীতির কেতাব আর দুর্লভ অমৃতসুধা এককাপ চা।
কিন্তু হঠাৎ একদিন ছেলেরা ইস্কুল যাবার পথ থেকে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এল। দেখতে দেখতে চৌধুরিবাড়ি থেকে সাত পাই পেরিয়ে উকিলপাড়া, মালগুদাম ছাড়িয়ে একদিকে মোক্তারপাড়া, অন্য দিকে নউল্যাপাড়া আর বড়ো পুকুরের পাড়গুলোতে কথাটা ছড়িয়ে পড়ল আগুনের মতো। মালগুদামের কুলিরা এল, আই. জি. এন. কোম্পানির মেয়ে-পুরুষ পাটের মুটে, ইস্কুলের ছেলেরা বেরিয়ে পড়ল। মেয়েদের ইস্কুলের বেড়া সরে গেল। ঘরের মেয়েরা পেছনের শানপাতা রাস্তা ছেড়ে সদর রাস্তায় এলেন। অগ্নিশিখার মতো একটি চলমান জনতা এসে থামল থানার বাইরে-ওদের ছাড়তেই হবে। বিয়াল্লিশের আগস্ট আন্দোলন শুরু হল নেত্রকোণা কাঁপিয়ে। কম্যুনিস্ট দাদারা নামলেন না সংগ্রামক্ষেত্রে। তবু যে ঘরের গৃহস্বামীরা গিয়েছেন, সেই ঘরের দায়িত্ব এসে পড়ল তাঁদেরই ঘাড়ে। দেখতে দেখতে পাড়া খালি হয়ে গেল। আদালতের সামনের পিকেটিং পাতলা হল, ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী সব যুবা গেল কারাগারে।
এখন চায়ের দোকান ম্লান। তারপর আবার নেত্রকোণার দিন এসেছিল। হাজংদের পদধ্বনি ভেসে এসেছিল গারো পাহাড়ের সানুদেশ থেকে। কিন্তু বিয়াল্লিশের পাঁচ বছর পর আবার প্রাণশক্তি দুর্বল হয়ে এল পাহাড়তলির শহর নেত্রকোণায়। নেত্রকোণার জীবনরস শুষে নিল তারই আরাধ্য দেবতা-ব্যভিচারী রাজনীতি।
এখন মাঝে মাঝে বুনো হাঁসের স্বপ্ন দেখি, আকাশ আঁধার-করা মেঘের ছায়া পড়ে মনে। এখনও ঢল নামে মগরায়। টিনের চালে শিশির ঝরে, কাঁঠালপাতা পড়ে টুপটাপ। এখনও এসব শুনি। অভয়দার দোকান, আমতলা–ধবলার পুলের পাড়ের সূর্যাস্ত, গুদারার ঘাটে হাটুরে মানুষের ভিড়। এখনও এসব দেখি। মনের দিগন্তে তারা আছে, দেশের সীমান্তে তারা দুরে।
.
বিন্যাফৈর
জননী আর জন্মভূমি–পৃথিবীর শেষপ্রান্তে বসেও মনে পড়ে, মন ভার হয়ে আসে, প্রাণ বলে যাই-যাই, আর একবার সেই ডোবার জলে ধ্যানী মাছরাঙার ঝাঁপ খাওয়া দেখে আসি।
বাংলাদেশের গ্রাম বলতে শুধু রামধনু রঙের আকাশ, বুনো ঘোড়ার মতো বর্বর বর্ষার নদী, মাঠভরা সবুজ ধানের ঢেউ বোঝায় না–সে-কথা জানার মতো বয়স এখন হয়েছে। অনেক দুঃখ দেখেছি, অনেক কান্না শুনেছি, অনেক মৃত্যু দেখেছি। জানি সেখানে ম্যালেরিয়ার সময় ঠিকমতো কুইনিন মেলে না, সুযোগ বুঝলে মহাজনের গোলায় রাতারাতি চালের বস্তা কাবার হয়ে যায়, ডাকাত পড়লে তোক এগিয়ে আসে না, ভালো একটা ইস্কুল নেই, ঝড়ে ঘরের চালা উড়ে যায়, ঝাঁঝরা টিনের ফাঁক দিয়ে অবিরলধারে বর্ষার জল পড়ে। সবই জানি। মন্বন্তরে আশপাশের কত বাড়ির ভিটে উজাড় হয়ে গেল। ভূতের ভয়ে-ভরা ছেলেবেলা থেকে রোজ রাত্রিতেই ঘুম ভেঙে দুখীরাম দফাদারের বাজখাঁই গলার হাঁক শুনে বুক দুর দুর করে উঠেছে। হাতে টিমটিমে লণ্ঠন, সাপের মতো লিকলিকে সড়কি, দুখীরাম হাঁক দিচ্ছে—’বাবু জাগেন?’ আজও যেন হঠাৎ এক এক রাত্রিতে সেই স্বর শুনতে পাই। গাঁজার টানে ঊর্ধ্বনেত্র হয়ে সন্ধ্যায় গুম হয়ে বারান্দায় বসে থাকত, সময়ে অসময়ে বউটাকে ধরে বেধড়ক পেটাত। নিঃস্ব নিরন্ন সেই ইস্পাতের মতো লোকটাকে পঞ্চাশ সালে খ্যাঁকশিয়ালরা রাতারাতি টেনে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলল। আর আমার মালিবউ মোক্ষদা–অফুরন্ত রূপকথার মায়াপুরী যে খুলে দিয়েছিল–ভাঙা কুঁড়ের নীচে সেকেলে এক নড়বড়ে খাটের তলায় খিদের জ্বালায় ধুঁকতে ধুঁকতে তার প্রাণের ভোমরা চুপ করল। তার গোছাভরা তাগাতাবিজ আর মন্ত্রের শক্তিতে বাঁধা পোষা ভূতের দল বাঁচাতে পারল না তাকে। কলকাতা থেকে সেবার গ্রামে গেলাম। চিরকাল যার বুকেপিঠে মানুষ হয়েছি, নিজে না খেয়ে কলাটা-মুলোটা রেখে দিত আমাদের জন্য সরিয়ে, সেই লোক আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে হাত ধরে কেঁদে বলল-”খোকন, বড়ো দুঃখ। পারিস তো চার আনা পয়সা আমাকে দিয়ে যা।’-এই সবই তো দেখেছি। তবু যেন আর একবার মন বলে যাই-যাই। ঝুমকোলতায় ঢাকা ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়ার ধারে সেই শূন্য উঠোনের তুলসীতলায় গিয়ে দাঁড়াই একবার। জননী আর জন্মভূমি–তার চাইতে আপনকরা প্রাণের জিনিস স্বর্গে গেলেও পাব না।
সেই দেশ চিরকালের মতো পর হয়ে গেল? মানচিত্রে একটা রেখার এক টানে নিজের বাড়ি হয়ে গেল বিদেশ?–ভাবতেও পারি না। আমরা রাজ্য চাইনি, রাজত্ব চাইনি, সরকারি খেতাবের গৌরব চাইনি। শিশুকাল থেকে মুসলমান প্রজার দেওয়া সুখ-দুঃখের টাকায় আমরা মানুষ হয়েছি–কিন্তু মনে মনে লজ্জা পেয়েছি সেজন্যে। প্রাণের তেপান্তরের খোঁজে মন্ডল সাহেবের আরবি-ঘোড়ায় চড়ে মাঠের পথে উদ্দাম হয়ে ছুটে বেড়ানোর সুখ এ জীবনে আর কি কখনো হবে?
কত মুখ মনে পড়ে! কচি, কাঁচা, ছেলে, বুড়ো, কার গালে দাড়ি, কার শিরে টিকি; পিঠে জাল কাঁধে লাঙল, মাথায় ঝাঁকা; ছিন্ন লালশাড়ি, গ্রন্থি-দেওয়া আধময়লা থান; কাকা, চাচা, দিদি, বউ-কতরকম সম্পর্ক। দ্যাশে আইলেন?’–একগাল হাসি। কী এক রকম খুশিতে মনটা লাফ দিয়ে উঠত নদীর ঘাটে স্টিমার থেকে নেমেই। মাল আছে না কর্তা? তাইলে ঘোড়া দেই এট্টা। গরম চমচম আছে বাবু, নিয়া যান কিছু। শরীর ভালো আছে ত?’-কে হিন্দু, কে মুসলমান? এরা সবাই আমার আপনজন। তারা আছে, তারা থাকবে। পৃথিবীর কোনো যুদ্ধ, কোনো দাঙ্গা, সে-কথা ভুলিয়ে দিতে পারবে না। তবু যখন দলে দলে নিরাশ্রয়ের দল চিরকালের ভিটে-মাটি ফেলে নিষ্ঠুর প্রবাসের গাঁয়ে প্রাণের মায়ায় ছুটে আসে, অভিমানে মন ভারী হয়ে ওঠে। কিন্তু অভিমান কার ওপর করব? যদি নিশ্চিন্ত মনে সে-কথা জানতুম!
নিজের জন্মভূমি, নিজের গ্রাম যে এত আমাদের প্রিয়, এত গরীয়সী সে কি শুধু অবুঝ মনের ভাবালুতা? সে কী শুধু দশের মুখের শোনা কথা? পৃথিবীর সবচেয়ে হতশ্রী পল্লিতে জন্মের জীর্ণ কুটিরটি নিজের চোখে যে তাজমহলের চেয়েও সুন্দর লাগে-তার মধ্যে ফাঁকি নেই। সেই বাড়িতে একদিন আমি চোখ মেলে অবাক-বিশ্বে প্রথম তাকিয়েছিলাম। বাতাবিলেবু ফুলের ঘ্রাণ চিনতে চিনতে গুনগুন করে মায়ের মুখে সেই বাড়িতে আমার রবীন্দ্রনাথের গান প্রথম শোনা। মালিবউ-এর হাত ধরে শঙ্কিত মনে সেই গ্রামের রাস্তা বেয়ে প্রথম পাঠশালায় যাওয়া। রহস্যে ভরা কলকাতা শহরের প্রথম চিঠি পাওয়া সেই বিন্যাফৈর গ্রামের ডাকপিয়োন আতোয়ার ভাইয়ের হাত থেকে। নদীর পাড়েতে দাঁড়িয়ে ধু-ধু চরের দিকে তাকিয়ে বিরাট বিশ্বের অস্ফুট স্বপ্ন দেখা। এসব কি ভোলা যায়? দু-চোখ ভরে, মন ভরে, হৃদয় ভরে আমার সেই আপন গ্রাম আমাকে অকৃপণভাবে কতই যে দিয়েছে। এই সুয়োরানির দেশ কলকাতা শহরের এত সুখ গলা দিয়ে যেন নামতে চায় না। ধড়ফড় করে এক সময় মন বলে ওঠে, যাই-যাই আমাদের সেই দুয়োরানি দুঃখিনী মায়ের কোলটিতে।
কলকাতা শহর থেকে আড়াইশো মাইল দূরে। ব্রহ্মপুত্রের শাখানদীর শাখানদী ঘুরে ঘুরে এঁকেবেঁকে গেছে। সে বড়ো সহজ ব্যাপার নয়। নদী তো আরও কত দেখলাম, কিন্তু সেরকমটি আর দেখলাম না। ফাল্গুন, চৈত্রে মরুভূমির মতো ধু-ধু করছে বালির চড়া, রোদূরে তাকিয়ে থাকলে মাথা ঝিমিঝিম করে। ওপারে বালির ডাঙা, মুসলমান চাষিদের বাস। কী দুর্দান্ত কষ্ট সহ্য করতে পারে কালো কালো বলিষ্ঠ সেই চাষির দল। তাদের মধ্যে বেঁটেখাটো সর্দার গোছের একটা লোক–”শাহেনশা’ নাম ধারণ করে দোর্দন্ড রাজত্ব চালাচ্ছিল সেই তখনকার ইংরেজ রাজত্বের কালে। প্রকান্ড একটা আস্ত চরের মালিক ছিল সে। রাস্তায় যখন চলত তখন তার সামনে পিছনে থাকত পঁচিশ-ত্রিশটি দেহরক্ষী সর্দার, কোমরে গামছা জড়ানো, মাথায় পাগড়ি, কাঁধে লাঠি। ফি-বছর দু-চারটি করে বিয়ে করত এবং বিয়ে করেই সেই অশিক্ষিত গ্রাম্য চাষির মেয়েদের সে রাইফেল ধরতে শেখাত। তাদের তৈরি করে নিত নিজের মনের মতো করে। কোনো পুলিশ, কোনো আদালতের সে তোয়াক্কা রাখে না। দশটি বছর ছায়ার মতো পিছনে ঘুরেও তার সন্ধান পায়নি সরকারের চরেরা। এই সেদিন শুনলাম পুলিশের শক্ত বেড়াজালে সে আটকা পড়েছে এতকাল পরে–রাইফেলধারী দুজন নতুন বিয়ে-করা স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে। এরা ভয়ংকর, এরা ভীষণ। এদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ থাকত সাত তল্লাটের লোক। তবু সে স্মৃতি ভালো লাগে।
স্টিমারঘাট থেকে আঁকাবাঁকা পথ–বিধবার সিঁথির মতো ম্লান, ধূসর। তারপরে খেলার মাঠ, তারপরে টিনের আটচালায় গ্রামের ইস্কুল, বাঁধানো-ঘাট পুকুর, কৃষ্ণচূড়ার গাছ, আবার সড়ক, সরু কাঠের পুল, সরষে খেতের ধার দিয়ে ঢুকে আমার গ্রামের গাছের ছায়া। আঃ গ্রীষ্মের বৃষ্টির মতো ঝরঝর করে সেই ছায়ার শান্তি যেন গলায় গায়ে মাথায় ঝরে ঝরে পড়ে। আর কত পাখি! শহরের লোক চেনে শুধু কাক আর চড়াই। কারও কারও খাঁচায় থাকে শিকল-বাঁধা কোকিল, বিরস সুরে বারোমাসই ডাকে। আর শহরে পাখি আছে আলিপুরের পশুশালায়। কিন্তু পাখি দেখতে, পাখি চিনতে কে বা যায় সেখানে? ওদিকে গ্রামে যখন মনমরা শীতের শেষে একদিন হঠাৎ ঝকঝকে গলায় কোকিল ডেকে ওঠে–আঃ, শত সহস্র প্রাত্যহিক দুঃখে-ভরা পৃথিবী যেন চিৎকার করে ওঠে আনন্দে। গ্রীষ্মের রাতে নির্লজ্জ ‘বউ কথা-কও’ ‘বউ-কথা-কও’ শুনতে শুনতে ঘুম ভেঙে জেগে উঠে আবার ঘুমিয়ে পড়ি। সাত সকালেই দোয়েল চুপিচুপি বসে গলা সেধে নিয়ে ফুড়ত করে দিনের কাজে বেরিয়ে পড়ে। ঘুঘু তখন কলমের ডালে বসে রোদকে সাধে—’সুয্যি ঠাকুর ওঠো-ওঠো-ওঠো।’
পূর্ববাংলার কোনো গৌরবই নেই আজ। কিন্তু কোমলে কঠোরে বিচিত্রতায় ভরা তার যে আপনকার রূপটি এই এ-যুগেও আমরা দেখেছি, আর কোথাও তার তুলনা নেই। যদি সম্ভব হত, এখনও যদি সম্ভব হয়, আবার কি তাহলে সেই নিভৃত পল্লিতে ফিরে গিয়ে দিন কাটবে, মন টিকবে? স্বীকার করি–টিকবে না। আরও শিক্ষিত, আমরা শহরের নেশার স্বাদ পেয়েছি। আমাদের জাত গেছে। তাই আমরা আন্তর্জাতিক। কলের জল আর পাউরুটি না হলে আমাদের মুখে রোচে না! বিজলি তারের আলো না জ্বললে আমাদের জীবন অন্ধকার। আমাদের জীবন জটিল হয়েছে। আমাদের প্রয়োজনের সীমা বেড়েছে। তা ছাড়া শহর আমাদের জীবিকা দেয়, শহরের ইস্কুলে আমাদের ছেলেরা পড়ে। পারব না, আবার সেই গ্রামে ফিরে যাওয়ার পথ চিরকালের মতো রুদ্ধ হয়েছে আমাদের জীবনে।
কিন্তু তাতে কী? সে যে আমার নিজের বাড়ি, নিজের ঘর! তারা যে আমার নিজের লোক। জীবিকার ধাঁধায়, জীবনের জটিল পাকে যতই আমরা ঘুরি না কেন, এক সময় তো ইচ্ছে করে ফিরে যাই মিটমিটে প্রদীপ জ্বালানো আপন বাড়ির ঘরটিতে! সেই আমার স্বপ্নে ভরা ছেলেবেলার দেশ। বোমায়, আগুনে, কামানে, বারুদে, যুদ্ধে, দাঙ্গায় পৃথিবীর অর্ধেক যদি ছারখারও হয়, তবু সেখানে থাকবে চুল-এলানো বাঁশবনের লুটোপুটি হাওয়া, কোজাগরী পূর্ণিমার মধুর রাত। টিনের আটচালায় সরসর করে পাতা ঝরবে। হিজলের ফুল ভাসবে পচা ডোবার জলে। সেই রবিবারে হাট বসবে। পাঠশালার বুড়ো মৌলবি সাহেব ওপারের চরের থেকে বেগুন-মুলো বেচতে আসবেন এ পারের গ্রামের বাজারে। কৃষ্ণের জীব বেতো ঘোড়ার পেটে-পিঠে তিনমন বোঝা দিয়ে গঞ্জের হাটে যাবে গাঁয়ের ব্যাপারীরা! বর্ষায় খেত ডুববে, ঝড়ে ভাঙা গাছের ডালে পথ বন্ধ হবে। কেউ তাকিয়ে দেখবে না, তবু সময় এলেই পুকুরের ধারে পলাশের ডাল লাল হয়ে উঠবে। বাবুই পাখিরা দোল খাবে নিপুণ ঠোঁটে-বোনা তাদের তালের পাতার দোলনায়। কিন্তু তারা কোথায়? যারা একদিন এপাড়া ওপড়ায় সাতপুরুষের ভিটে আঁকড়ে পড়েছিল? সেই দলাদলি, নিন্দা, ঈর্ষা, মন্দ আর অফুরন্ত ভাললাতে ভরা তারা
কোথায়?
সময় অস্থির, জীবন অস্থির। যারা গেছে তাদের আর এ জীবনে খুঁজে পাওয়ার সময় হবে না।
.
কমলপুর
আমি একজন সাধারণ মানুষ। আপনাদের সাধারণতন্ত্রের পুরোপুরি নাগরিকও নই। কারণ, নাগরিক-গৌরবের অধিকারী হবার পূর্ণ যোগ্যতা নেই বলেই হয়তো চিনবেন না আমাকে, অন্তত চেনবার মতো সময়, সুযোগ ও প্রয়োজনবোধও নেই হয়তো আপনার। কিন্তু আপনি আমাকে দেখেছেন, শুধু আমাকে নয়, আমার মতো হাজার হাজার গৃহহীন উদবাস্তু ছন্নছাড়াদের কলকাতায় ও তার আশপাশের শরণার্থী শিবিরে কিংবা ভাঙা বস্তির অন্ধ কুটিরে; না দেখলেও কাগজে নিশ্চয় পড়েছেন তাদের খবর।
কলকাতার সঙ্গে নাড়ির যোগ নেই আমার, আছে প্রয়োজনের। বিপর্যয়ের পসরা মাথায় বহন করে যেদিন এসেছিলাম কলকাতায়, তখন এই মহানগরী নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যে আমায় ঠেলে বের করে দিতে চেয়েছিল তার আঙিনা থেকে। দাবি তো আমার বেশি কিছু ছিল না। আট নম্বর থিয়েটার রোডের বাড়িটাও আমি চাইনি, কিংবা পারমিটের জন্যে আবেদন নিবেদনও করিনি রাজ্যসচিবদের কাছে। চেয়েছিলাম একটু মাথা গোঁজবার জায়গা আর সাধারণ সুস্থ নাগরিকের মতো খেয়ে-পরে থাকবার অধিকার। কলকাতায় ধনভান্ডার দিন দিন স্ফীতকায় হয়ে উঠছে ক্লাইভ স্ট্রিট বড়োবাজারের হর্ম্যাভ্যন্তরে। সে ভান্ডারের অংশীদার হতে তো চাইনি আমি। আমি চেয়েছিলাম নেহাৎ জীবনধারণের মতো আয়, কায়িক ও মানসিক শ্রমের বিনিময়ে। নিষ্ঠুর নগর-লক্ষ্মী রূঢ়ভাবে প্রত্যাখান করেছে আমায় বারবার। তবুও নিরাশ হইনি আমি! জীবিকার জন্যে চ্যালেঞ্জ করেছিলাম কলকাতাকে। সে আমাকে হারাতে পারেনি। তাই আজও বেঁচে আছি আপনাদের শোনাব বলে আমার ফেলে-আসা জীবনের ইতিহাস, যা জড়িত হয়ে আছে আমার সাতপুরুষের ভিটে ছেড়ে-আসা গ্রামের সঙ্গে।
।মেঘনার কোলঘেঁষা পূর্ববাংলার একটি গ্রাম। পৃথিবীতে প্রথম যে আকাশের নীল আর সূর্যের আলো এসে লেগেছিল আমার চোখে, সেটি সেই গ্রামের। স্বপ্নের মতো লাগত গ্রামের প্রতিটি রাস্তা, প্রতিটি মাঠ, প্রতিটি পুকুরের চারধারের প্রকৃতির পরিবেশকে। পশ্চিমবাংলার অনেক গ্রাম দেখেছি। কিন্তু পূর্ববাংলার গ্রামের মতো সবুজ স্নিগ্ধ মাটির স্পর্শ কোথাও পাইনি। যে গ্রামে জন্মেছিলাম, তার আয়তন ক্ষুদ্র, জনবল নগণ্য। হয়তো পাঁচ হাজারের বেশি হবে না। নগণ্য বললাম এইজন্যে যে, পূর্ববাংলার যেকোনো গ্রামে দশ হাজার লোকের বসবাস অত্যন্ত স্বাভাবিক। গ্রাম থেকে একমাইল দূরে উদ্দাম স্রোতোধারায় বয়ে চলেছে দূরন্ত মেঘনা। কালো মেঘের ছায়া বুকে নিয়ে ভরা বর্ষায় সে কী দুর্দাম, দুর্বার তার গতি! একবার মনে আছে ছোটোবেলায় পাড়ি দিয়েছিলাম মেঘনা, ছোট্ট নৌকা করে। ঢেউয়ের ঝাঁপটা লেগে নৌকা প্রায় তলিয়ে যায়। আমার কিশোর মন সেদিন ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মেঘনা নদীর মুসলমান মাঝি ঢেউকে ভয় পায় না। দরিয়ার পিরের দোহাই দিয়ে নির্বিঘ্নে পৌঁছে দিয়েছিল সে আমাকে নদীর ওপারে। বিদ্রোহী মেঘনার সেদিনের রূপটি মনের স্লেটে খোদাই করা আছে আজও। সেই মেঘনার স্মৃতি নিয়ে সুবর্ণরেখা, অজয় কিংবা কোপাই নদী দেখলে মনে হয়, এগুলো নদী নয়, নদীর ছায়ারূপ।
যে গ্রামে জন্ম, সেখানে সব সময় থাকতাম না আমি। মাইল ষোলো দূরের একটা আধা শহর বৃহত্তর গ্রামের ইস্কুলে পড়তাম আমি আমার মা-বাবার সঙ্গে থেকে। ছুটিতে চলে আসতাম বাড়িতে। রেলস্টেশন ছিল একমাইল দূরে। পরে অবশ্য গ্রামের মধ্যে স্টেশনটি স্থানান্তরিত হয়ে এসেছিল রেল কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনে। স্টেশন থেকে হেঁটে গ্রামমুখো আসবার সময়টা যেন আর কাটতে চাইত না। কতক্ষণে সুপুরি গাছের সারের তলা দিয়ে বাঁকা পথটি ধরে বাড়ির উঠোনে এসে হাঁক দেব ঠাকুরমাকে, সেজন্যে মনটা উন্মুখ হয়ে থাকত। গ্রীষ্মের ছুটিটাকে আমরা বলতাম আম-কাঁঠালের ছুটি। কাঁচা আমের গন্ধে তখন গ্রামের আকাশ ভরপুর। কিছুদিন পরেই রং ধরতে শুরু করবে গাছগুলোতে। ঘুঘু-ডাকা এক-একটা দুপুর। কত দুরন্ত মধ্যাহ্ন কাটিয়েছি কাঁচামিঠে আমগাছের ওপরে, সেগুলো আজ স্মৃতিমাত্র। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা সামনের ধানখেতের উদার বিস্তারকে মনে হত রাত্রিবেলা ঠাকুরমার কাছে শোনা রূপকথার সেই তেপান্তরের মাঠের মতো। কতদিন যে আশা করেছি, দেখা হয়ে যাবে নীল ঘোড়ায়-চড়া রাজপুত্রের সঙ্গে!
স্নান করতে যেতাম দক্ষিণের বিলে কিংবা কোনো কোনোদিন পঞ্চবটির ঘাটে। ঘাটটিতে পাঁচটি বটগাছ ছিল বলেই নামকরণের এত ঘটা। গ্রীষ্মের শেষে বিল যেত শুকিয়ে, তবু সেই কাদাভরা বিলের জলেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি। শালুক আর পদ্মলতার অরণ্য ছিল বিলটিতে। সাঁতার কাটতে গিয়ে অনেকবার লতায় জড়িয়ে যেত পা। তবু আমাদের দুরন্তপনার শেষ ছিল না। গ্রামটি ক্ষুদ্রায়তন হলেও এর মধ্যেই নানা পল্লিতে ভাগ করা ছিল তার অধিবাসীদের বাসস্থান। পূর্বদিকে ছিল আচার্যপাড়া, দক্ষিণে ছিল জেলেপাড়া, উত্তরে তাঁতিদের বাসস্থান, তারই পাশে ছিল মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের বাড়ি, পশ্চিমে ছিল মুসলমান চাষিদের পাড়া। প্রতিসন্ধ্যায় এক-একটা পাড়ার এক-একটা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ত। জেলেদের ঘরে জন্মেছিলেন বৃন্দাবন। আমরা তাঁকে দাদা বলে ডাকতাম। তিনি ছিলেন কবিয়াল। তারাশঙ্কর বাবুর কবি’ যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা সেই কবির জীবনীটি মনে করে দেখুন। এ কবিকে আমি চোখে দেখেছি। তাঁর সান্নিধ্য পেয়ে ধন্য হয়েছিল আমার কিশোর মন। তিনি ছিলেন বৈষ্ণব।
দোল-উৎসবে, ঝুলনযাত্রায় আমরা বহুবার বৃন্দাবনের কণ্ঠে কবিগান শুনেছি। বাংলার লুপ্তপ্রায় কবি-সংস্কৃতির শেষপর্যায়টুকু আমরা শুনেছিলাম তাঁর গানে। তিনি আজ নেই। তাঁর গানের স্মৃতি বেঁচে আছে। দুর্গাপুজোর উৎসবের স্মৃতি আজও অমলিন। বারোয়ারি পুজোয় চাঁপার ডালে ভিড় করত এসে দোয়েল। দুর্গা পুজোর সে কী উদ্যম আর উদ্যোগ। বর্ষ পরিক্রমা করে আশ্বিনের এই দিনগুলোর জন্যে, উৎসব-বিলাসী গ্রামের ধনী-নির্ধন অধিবাসীরা প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে থাকত। শরতের সোনালি আঁচল ছড়িয়ে পড়ত আকাশের গায়। পেঁজা তুলোর মতো নির্জলা মেঘের দল উধাও হয়ে যেত মেঘনার দু-তীরের আকাশে। নদীর চরে একরাশ সাদা কাশবনের ভেতর যেন হারিয়ে যেত মন। রাস্তার দু-ধারে অযত্ন-বর্ধিত কেয়া আর জুইফুলের ঝোপে মন-পাগলকরা গন্ধ ছড়িয়ে থাকত। শিবতলার মন্দিরের গা বেয়ে যে মাধবীলতার মালঞ্চ নুয়ে পড়েছিল মাটিতে তার সৌরভ পথ-চলা হাটুরে লোকদের মনকেও দিত ভরিয়ে। গ্রামের বাড়িতে বারোমাসে তেরো পার্বণের প্রথা প্রচলিত পূর্ববাংলার সবখানেই। সেই উৎসবের আনন্দ শুধুমাত্র হিন্দুদের ছিল না, আমাদের মুসলমান প্রতিবেশীদেরও ভাগ নিতে দেখেছি তাতে সমানভাবে। দুর্গাপুজো কিংবা লক্ষ্মীপুজোর সময়ে মুসলমান ভাইবোনদের জন্যে খাবার আলাদা করে রাখত গৃহকর্তারা। আমাদের মতো মধ্যবিত্তদের খেত-জমিগুলো ভাগে চাষ করত মুসলমান কৃষকেরা। তাদের বলা হত বর্গাদার। কয়েকজন বর্গাদার কৃষকের নাম আজও মনে আছে আমার। সুন্দর আলি, রহিমউদ্দিন, সুকুর, মামুদ। এরা সবাই আমাদের বাড়িতে আসত। পরমসম্প্রীতি আর প্রতিবেশিত্বের মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ওদের সঙ্গে। আমার ঠাকুরমা ওদের ভালোবাসতেন ছেলের মতো। কোনোদিন ভাবিনি এমনি করে তাদের ছেড়ে চলে আসতে হবে অভাবনীয় ভয় আর আতঙ্ক নিয়ে।
গ্রামের বাজার ছিল একমাইল দূরে। মেঘনার তীরে সেই বাজারটি পূর্ববাংলার অন্যতম বৃহৎ ব্যবসায়স্থল ও বন্দর। স্থানীয় অধিবাসীদের চেষ্টায় সেখানে স্কুল ও কলেজ দুই-ই স্থাপিত হয়েছে। আজ জানি না সেখানে শিক্ষা ও সংস্কৃতির উত্তরসাধক কারা।
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জাপানি-অভিযানের আশঙ্কা ছিল পূর্ববাংলার প্রান্ত দিয়ে। চট্টগ্রামে প্রতিরোধের আয়োজন করেছিল সাউথ-ইস্ট এশিয়া কমাণ্ডের সৈন্যদল। রণসম্ভার ও সৈন্যবাহিনী চলাচলের জন্যে আমাদের গ্রামের স্টেশনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। বিশেষ করে মেঘনার ওপরে যে সেতুটি আছে তা রক্ষা করবার জন্যে বিমানবিধ্বংসী কামানও সজ্জিত করে রাখা হয়েছিল সেখানে। সেই রণসজ্জার পাশে গ্রামটির নিরাভরণ শান্তশ্রী কী অপূর্বই না লাগত! নির্মেঘ আকাশে তখন সন্ধানী বিমানের আনাগোনা থরথর করে কাঁপিয়ে দিয়ে যেত গ্রামের মাটিকে, তার ভাঙা শিবমন্দির আর পঞ্চবটির ঘাটকে।
যুদ্ধের সমাপ্তিতে সে কাঁপনের অবসান ঘটল। আবার বারোয়ারিতলায় দুর্গাপুজোর উৎসবে বসল যাত্রার আসর। স্তব্ধ-কুতূহলী শ্রোতাদের চোখেমুখে তখন নিমাই সন্ন্যাসের করুণতার ছায়া এসে নেমেছে। ছলছল করছে সহস্র জোড়া চক্ষু। তাকিয়ে দেখলাম, কোণে-বসা। রহিমউদ্দিনের চোখেও জল। নিমাই সেদিন জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলকে কাঁদিয়ে দিয়েছিল।
এই ছিল গ্রামের স্বরূপ। এ গ্রামকে ভালোবেসেছি। তার সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি, অজ্ঞতা, কুসংস্কার নিয়েই ভালোবেসেছি। নিরক্ষর কৃষক, তন্তুবায় প্রভৃতি যেমন ছিল সেখানে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্তদের সংখ্যাও কম ছিল না। আলো আর অন্ধকার পাশাপাশি হয়েই বাস করছিল সে গ্রামে। কে জানত অকস্মাৎ কালবৈশাখীর ঝড় এমনি করে আলোকে নিভিয়ে দিয়ে নিরন্ধ্র অন্ধকারের কালিমা ছড়িয়ে দেবে সারাআকাশময়। সেই অন্ধকার আকাশের নীচে দুঃস্বপ্নের মতো পড়ে আছে আমার ছেড়ে-আসা গ্রাম, ময়মনসিংহ জেলার দক্ষিণ প্রান্তে মেঘনা নদীর তীরবর্তী সোনার কমলপুর। তার এক মাইল দূরে ভৈরববাজার আর ষোলো মাইল দূরে আধা-শহর বাজিতপুর। হায় রে জন্মদুঃখিনী দেশ, শিশু-ভোলানো প্রবোধ দিয়ে সেদিন তোমাকে ছেড়ে চলে এলাম কলকাতার ফুটপাথকে আশ্রয় করে। কে জানে তোমার আকাশে এখনও চাঁদ আর তারা হাসছে কি না, কে জানে মেঘনার দোলনে কাঁপছে কি না তোমার ঝুমকোলতার দুল আর দোলনচাঁপার কণ্ঠহার।
স্টেশন থেকে বাড়ি আসবার পথে কতজন কুশল প্রশ্ন করত। আর আজ আমি হারিয়ে গেছি কলকাতার জনারণ্যে, হারিয়ে গেছি সুরেন ব্যানার্জি রোডের আস্তানায়। এখানে আমায় কেউ চেনে না, কেউ শুধোয় না–হে বন্ধু, আছ তত ভালো? আমি তো এখানকার অধিবাসী নই, আমি যে শরণার্থী, উদবাস্তু।
.
খালিয়াজুরি
গ্রামহৃদয়া বাংলাদেশ। এ দেশের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আমার মতো লক্ষজনের আশৈশবের স্মৃতি। এর প্রতিটি ধূলিকণা, এর আকাশের রংফেরা, এর নদী-কল্লোলের পরিচিত সুর একান্ত করে ভালোবেসেছি, ভালোবেসে ধন্য হয়েছি। কতদিন মনে হয়েছে এ দেশের মাটি শুধু মাটি নয়, মায়ের মতোই এ মাটি স্নেহ-স্নিগ্ধ।
এ মাটির স্নেহ-দাক্ষিণ্যে প্রতিপালিত আমার সাতপুরুষ, হয়তো এই মাটিকেই আপন করে নিত আমাদের অনাগত উত্তর-পুরুষেরাও। কিন্তু আজ সে আশা স্বপ্ন বলেই মনে হয়। আমার জননী, আমার জন্মভূমি থেকে আজ আমি বিচ্ছিন্ন। আমি আজ প্রবাসী। কিন্তু দূরান্তরে থেকেও তো সে মাটির স্মৃতিকে ‘বিস্মৃতির মুক্তিপথ দিয়ে বিদায় করে দিতে পারছি না। গভীর রাত্রে যেমন করে ‘নিশি ডাকে’ বলে লোকপ্রসিদ্ধি আছে, তেমনি করে এই বিভুই-বিদেশে দেশের মাটি আমাকে নিশির ডাকের মতোই প্রতিদিন আকুল সুরে ডেকে বলছে, ওরে আয়, আয়, আয়।
গ্রামটি নেহাতই ছোটো। আকারে আয়তনে ছোটো হলেও শিক্ষায়-সংস্কৃতিতে, যশে গৌরবে, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে পূর্ব-ময়মনসিংহের এই গ্রামটি কিন্তু কোনোক্রমেই নগণ্য নয়।
কবে যে এখানে বাসস্থান গড়ে উঠেছিল তার সঠিক স্মৃতি বা ইতিবৃত্ত নেই। পন্ডিতেরাও এর সাল-তারিখ নিয়ে কোনোদিন তর্ক করেন না। যেটুকু শ্রুতি আছে তাও ক্রমে লোপ পেতে বসেছে। কারণ বহুপুরুষ অতিক্রম করে এসে তার প্রতি আমাদের ঔৎসুক্য কমে আসছে। কিংবদন্তি মতে মোগল রাজত্বের শেষের দিকে দক্ষিণ রাঢ় থেকে দুই ভাই পশুপতি ঠাকুর ও গণপতি ঠাকুর নিজেদের স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতা বজায় রাখবার জন্য মুসলমানদের সঙ্গে রণে ভঙ্গ দিয়ে জলপথে পলায়ন করে এসেছিলেন। বহুদেশ অতিক্রম করে প্রথমে খালিয়াজুরি গ্রামে তাঁরা বাসস্থান নির্মাণ করেন। এই স্থানটি জনবিরল এবং বর্ষায় একটি ছোটো দ্বীপের আকার ধারণ করে বলেই হয়তো তাঁরা এ স্থানটিকে নিরাপদ বলে মনে করেছিলেন। হয়তো বা বাসস্থানের পক্ষে যথেষ্ট মনে না হওয়ায় কিছুকাল মধ্যেই গণপতি ঠাকুর নতুন বাস্তুর সন্ধানে নির্গত হয়ে পাশের গ্রামে এসে আস্তানা গাড়েন। আর পশুপতি খালিয়াজুরিতেই থেকে গেলেন।
এই বাসস্থান নির্বাচনের মূলে নিরাপত্তার প্রশ্নটা যেমন ছিল, তেমনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও প্রাচুর্যের আবেদনও যে ছিল, একথা অনুমান করা যেতে পারে। একদিকে কলস্বনা নদী বেত্রবতী, চলতি কথায় যাকে বলে বেতাই’–অপরদিকে বিস্তীর্ণ জলরাশি, মাঝখান দিয়ে সুপরিসর নদীতটরেখা–বাসস্থানের যোগ্য স্থানই বটে। নদীকে পেছনদিকে ফেলে বাড়ি নির্মিত হল–সম্মুখের অঞ্চল জুড়ে আয়োজন হল আবাদের। তারই শেষ প্রান্ত থেকে বিস্তীর্ণ বিলের অপর তীরে সুর্যোদয় এক লোভনীয় প্রাকৃতিক পটভূমি সৃষ্টি করে। নদীর পশ্চিম তীরটি অপেক্ষাকৃত ঢালু এবং বনজঙ্গলময়। কিছুদূরে কয়েক ঘর হদির বাস। হদি’রা এখন আর নেই, কবে কোন অতীতে যে তাদের বাসস্থান শূন্য হয়ে গেছে তার ইতিহাসও কেউ বলতে পারে না। তবে ক্রমে এই গণপতি ঠাকুরের বংশধরেরাই নদীর পশ্চিম তীরেও বসবাস আরম্ভ করেছিল এবং বিরাট জনপদ গড়ে তুলেছিল। কালক্রমে শুধু আদি বাড়িটাই পূর্বতীরে থেকে যায়, আর সবাই পশ্চিম তীরেই পল্লি গড়ে তোলে। এর মাইল দুই দূরেই ‘রোয়াইল বাড়ি’র ভগ্নাবশেষ আজও বিদ্যমান। বিরাট রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ–চতুর্দিকের পরিখা আজও একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। বহুভগ্ন বা ভূগর্ভনিমজ্জিত অট্টালিকা আজও পূর্ব পরিচয়ের সাক্ষ্য দিচ্ছে। সিংহদ্বারের দু-পাশে দুটি বিরাট দীঘি। এটি ছাড়াও অন্দরমহলের সংলগ্ন তিনটি পুকুর এবং দু-তিনটি স্ফটিকস্তম্ভও দেখতে পাওয়া যায়। প্রায় অর্ধমাইল পরিবৃত স্থান ইষ্টক-সমাকীর্ণ। কোনো কোনো ইটের গায়ে ফুল লতাপাতা খোদিত। কোনো কোনো ইট আবার চিনামাটির মতো একপ্রকার জিনিস দিয়ে তৈরি এবং তাতেও অপূর্ব শিল্পকলার নিদর্শন বর্তমান।
কিংবদন্তি মতে বিশ্বকর্মা স্বয়ং ছদ্মবেশে এই বাড়িটি গড়ে তুলছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে যাওয়ায় লাফ দিয়ে প্রাসাদ-শীর্ষ থেকে নীচে নেমে আসেন। সেই সময়েই নাকি বাড়িটি ভূতলে প্রবেশ করে। যে স্থানটিতে বিশ্বকর্মা পড়েছিলেন বলে প্রবাদ, সে স্থানটি একটি ছোটোখাটো জলাভূমিতে পরিণত হয়ে আছে এবং চলতি কথায় তাকে বলা হয় ‘কোর’।
অতীতের কথা থাক। সে দিনকাল তো অনেক আগেই গিয়েছে। কোনো এক ভূমিকম্পের পর থেকেই নাকি বেতাই নদীরও অন্তিম দশা দেখা দিয়েছে। যে ব্রহ্মপুত্র থেকে বেতাই নদীর উৎপত্তি, এখানে তার মতোই এই নদীটিও আজ একটি মরা নদী।
পাকিস্তানের বিপাকে পড়ে মুমূর্য গ্রামটিরও আজ অন্তিম অবস্থা। তবু তার কথা বলতে পারছি না। এই গ্রামখানিই যেন আমার সমস্ত সত্তাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। বিষয় সম্পত্তির প্রলোভন বা তার ক্ষতির বেদনায় নয়–যে আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছি, যে মধুর পরিবেশের মধ্যে আমার বিকাশ হয়েছে, তার মাধুর্যময় স্মৃতিটুকুই সে মাটির দিকে মনকে টেনে নেয়। বেতাইকে স্মরণ করে বলতে ইচ্ছে হয়, ‘সতত হে নদ তুমি পড়ো মোর মনে কিংবা গ্রামখানিকে স্মরণ করে ‘মোদের পিতৃ-পিতামহের চরণধূলি কোথায় রে’ বলতে যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি। মরা নদীর তেমন কোনো আকর্ষণ নেই–বৎসরের বেশির ভাগ সময়ই সে তার স্থির জলরাশি নিয়ে অসাড় হয়ে পড়ে থাকে। বৈশাখ মাসে অনেকটা তো শুকিয়েই যায়। তবে বর্ষায় আবার যৌবন-জোয়ার দেখা দেয়–দেখা দেয় নিস্তরঙ্গ জলরাশিতে স্রোতের প্রবল বেগ। কূল ছাপিয়ে জল বয়ে যায় ধানের খেতে খেতে। কচি ধানের পাতাগুলো যখন সোনালি রোদ্দুরে বাতাসে বাতাসে ঢেউ খেলে যায় তখন কতদিন আপন মনে আবৃত্তি করেছি–এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে।
নদীর তীরে হাট, তার পিছনে একটি পুকুর, তার উলটো দিক থেকেই গ্রামের আরম্ভ। একটি বটগাছ কোন অতীতকাল থেকে যে পারঘাটায় হাট-যাত্রীদের বিশ্রামের আয়োজন করে বসে আছে তা কেউ বলতে পারে না। এই বটবৃক্ষের নীচেই বর্ষাকালে ব্যাপারীদের নৌকাও এসে লাগে। গ্রামে সাড়া পড়ে যায়, চাঞ্চল্যের মরসুম পড়ে যায় পাট-ধান-মশলা ইত্যাদি বেচাকেনার। দূরদেশ থেকে আত্মীয়স্বজনের নৌকাও এসে লাগে। ছোটো ছেলের দল তামাশা দেখতে জড়ো হয়–যুবকের দল নিজেরা নৌকা চালিয়ে বেরিয়ে পড়ে আনন্দে। ছোটোবেলায় কতদিন যে নিজেরাও এমনি করে নৌকা নিয়ে মাতামাতি করেছি তার স্মৃতি মন থেকে এখনও মুছে যায়নি।
দীর্ঘকাল হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিতভাবেই পাশাপাশি বসবাস করে আসছে এই গ্রামে। তাদের পরস্পরের মধ্যে একটা প্রীতির ভাবের আদান-প্রদান ছিল। খেলাধুলায়, ষাঁড়ের লড়াইয়ে, গানে-বাজনায় সকলে একসঙ্গে আনন্দ করেছে–কোনোদিন ধর্মের গোঁড়ামি কাউকে পেয়ে বসেনি। একবার গ্রামে দাঙ্গার সময় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন হিন্দু-মুসলমান মিলিত হয়ে ভ্রাতৃবিরোধ রোধ করেছিল। সে-কথা আজ বারবার মনে পড়ছে।
স্মৃতির প্রেক্ষাপটে অতীত আজ মুখর হয়ে উঠছে। অনেক ভুলে-যাওয়া পরিচিত মানুষকে ফিরে পাচ্ছি। মনে পড়ছে সহরালি মাতব্বরের কথা–এই দীর্ঘাবয়ব, লম্বা ও পাকা চুল-দাড়ি; লোকটির চেহারায় যেমনি একটা সৌষ্ঠব ছিল, তেমনি ছিল ব্যক্তিত্বের ছাপ। তার অমায়িক প্রকৃতি, তার বিনম্র ব্যবহার, তার সুমিষ্ট সদালাপ ভুলে যাবার নয়। মনে পড়ে মনোহর ব্যাপারীর কথা। লাঠিখেলায় সে ছিল ওস্তাদ এবং সাহসও ছিল প্রচুর। সর্বদাই একটি দীর্ঘ লাঠি হাতে নিয়ে চলাফেরা করত এই লোকটি এবং যৌবনের দুঃসাহসিক কাহিনি অভিনব ভঙ্গি সহকারে শুনিয়ে আসর মশগুল করে তুলত। তারপর মনে পড়ে আলম মুনশির কথা। মুনশি হিসেবে এ অঞ্চলে বহুদূর পর্যন্ত তার একটা প্রভাব গড়ে উঠেছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই তা গড়ে উঠেছিল তার চরিত্রমাধুর্যে। আজ এরা কেউ আর জীবিত নেই। এদের উত্তরাধিকারীরাও সেসব সদগুণাবলির উত্তরাধিকার পায়নি কেউ। তা যদি পেত তবে এত সহজে গ্রামের এত পরিবর্তন হতে পারত না। মুনশির ভাইপো মুনশি হয়েছে বটে, কিন্তু এই জামু মুনশি তার চাচার ঠিক বিপরীত। তাকে লোকে সমীহ করে–শ্রদ্ধায় নয়, অন্তরের টানেও নয়–অনেকটা শনির সিন্নি-দেওয়া গোছের ব্যাপার। জামু মুনশিই এ অঞ্চলে লিগের পান্ডা, ইসলামের ধ্বজাবাহক এবং সাম্প্রতিক উস্কানির উৎস। সে কি যেমন তেমন মুনশি? গোটা পাঁচ-ছয় নিকে সে করেছে এবং তার চাচিকেও সে বাদ দেয়নি।
অবিনাশদারও সেদিন আর নেই। তিনি লাঠি হাতে নিলে একাই ছিলেন এক-শো। এত বড়ো শক্তিশালী পুরুষ এ অঞ্চলে আর ছিল না–এখন বৃদ্ধ স্থবির। আর সেই প্রসন্ন চক্রবর্তীর কথা। হাস্য-পরিহাসের জন্যে তিনি সকলের ছিলেন ঠাকুরদা। তাঁর বিরাট দাড়ি দেখে আমরা তাকে ডাকতাম ‘পশম ঠাকুরদা বলে। তারপর মনে পড়ে উল্লাস পন্ডিতের কথা। এই উল্লাস জাতিতে রজক দাস–লেখাপড়ার কোনো ধারই সে ধারেনি, নামটি পর্যন্ত সে লিখতে জানে না। তবুও সে পন্ডিত। লোকটির উপস্থিত বুদ্ধি ও হাস্যরস পরিবেশনের শক্তি অসাধারণ! যে কোনো স্থানে সে আসর জমিয়ে তুলতে পারে। তাকে ছাড়া কোনো গানের আসর জমে না। একদিন জিজ্ঞেস করলাম-‘কী রে উল্লাস, তুই লেখাপড়া জানিস না তো পন্ডিত হলি কি করে?’ সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল—’বাবু! আমি কি লেখাপড়ার পন্ডিত? আমি কথার পন্ডিত, হাসি-তামাশার পন্ডিত।’
প্রায় রোজ রাত্রেই বাউল গানের আসর বসত আমাদেরই বাড়িতে। এতে হিন্দু-মুসলমান সকলেই যোগ দিত। বঙ্গ-বিভাগের কিছুকাল পরেও চলেছিল এই আসর। গ্রাম্য জীবনের সেই বিমল আনন্দময় মুহূর্তগুলো আজ দুঃখের সঙ্গে মনে পড়ে। মনে পড়ে সকাল-বিকালের গল্পের আসরে তারাসুন্দরদার পান্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা, হুঁকো হাতে বিরাট গোঁফে চাড়া দিয়ে দ্বিজেন ডাক্তারের গল্প বলার অভিনব ভঙ্গি। তাস-পাশা-দাবার আসর–খেলাধুলার বৈকালিক আনন্দোৎসব, সেসব কি আর মন থেকে মুছে যেতে পারে?। আর সেই সঙ্গে মনে পড়ে ছিপ হাতে করে দল বেঁধে বঁড়শিতে মাছ ধরার অভিযানের কথা। ছোটোবেলায় আমরাও গিয়েছি বহুদিন। একালেও ছেলেরা যেত সেই বেতাই নদীতে, গাঁয়ের এ-পুকুর সে-পুকুরে বা ‘বগাউড়া’ বিলে কিংবা জোঁকার হাওরে। এই বগাউড়া বিলের সঙ্গে রায়বংশের একটি কিংবদন্তি জড়িত। বাড়ির ঠিক পিছনের সীমানা থেকেই এ বিল আরম্ভ হয়েছে বলা চলে। অতীতে এই বংশের লোকেরা নাকি অতিকায় ছিলেন–এত বিরাট বলিষ্ঠ চেহারা এ অঞ্চলে নাকি আর ছিল না। কয়েক পুরুষ পূর্বে মুকুন্দ রায়ের সুপ্রশস্ত বক্ষপটের মাপে একখানা ‘পদ্মপুরাণ’ পুস্তকের মলাট তৈরি করা হয়েছিল। প্রায় পৌনে একহাত লম্বা এই মলাটখানি এখনও তাঁর বিরাট চেহারার সাক্ষ্যস্বরূপ বিদ্যমান। মধ্যাহ্নভোজনের পর রায়েদের সেঁকুরের শব্দে বিশ্রামরত বকগুলো নাকি বিল থেকে যেত উড়ে এবং তাই থেকেই নাকি এর নাম হয়েছে বগাউড়া (বগা = বক) বিল। আর জোঁকার হাওর-বৈশিষ্ট্যে এ বিল বোধ হয় বাংলাদেশে অদ্বিতীয়। এ বিলে অসংখ্য জোঁক সর্বদা কিলবিল করে বেড়ায়-বর্ষায় নতুন জল যখন আসে তখন সেখানে পা দিলে একমিনিটেই জলের নীচের সমস্ত অংশটি জোঁকে ভরে যায়। এই জোঁকের জন্যেই বোধ হয় এরূপ নামকরণ হয়ে থাকবে এ জলাশয়ের। কিন্তু আসল বৈশিষ্ট্য এর মাটিতে। এত এঁটেল মাটি অন্য কোনো স্থানে পাওয়া দুষ্কর। বর্ষায় এ মাটি পায়ে এমনভাবে জড়িয়ে যাবে যে, সহজে ধুয়ে তোলা যায় না। গ্রীষ্মে পাথরের মতো শক্ত, কোদাল দিয়ে কাটা যায় না। বজ্ৰাদপি কঠোরানি মৃদুনি কুসুমাদপি’ কথাটা যদি মাটির বেলায় প্রয়োগ করা যায়, তাহলে এই জোঁকার হাওর সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা চলে। গ্রীষ্মকালে সমস্ত বিলটি ফেটে চৌচির হয়ে যায়। তখন এর মাটি কাটার মজুরও পাওয়া যায় না! মজুররা বলে জীবনে তারা এমন মাটি দেখেনি। ফাটলের ভেতর কোদাল চালিয়ে পাথরের টুকরোর মতো এক-একটি টুকরো বার করতে হয়। এ সবই এখনও তেমনি আছে, শুধু নেই আমরা।
.
বারোঘর
বহুদুঃখের মধ্যেও স্মৃতিঘেরা অতীতকে মনে পড়ে। বিগত দিনের সুখ, আনন্দ উৎসব আজ লাঞ্ছিত জীবনেও কেন মাথা ছুঁড়ে বড়ো হয়ে দেখা দিচ্ছে জানি না। কলকাতা মহানগরীর প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে কেন যেন কেবলই আমার গ্রামের চাষিদের ছোটো ছোটো শান্তিনীড় খড়ের ঘরের ছবিই ভেসে উঠছে বারবার। সেই খাল, কে কবে কেটেছিল জানি না, কিন্তু বর্ষার নতুন জলে খালের প্রাণে যে জোয়ার জাগত আজও তা স্পষ্ট মনে রয়েছে। নতুন বর্ষার জলনিকাশের খাল দিয়ে যে দেশের মধ্যে রাজনৈতিক কুমির এসে মানুষকে ঘরছাড়া করবে তা আগে কে ভাবতে পেরেছে! স্বস্তিতে ভরা আমাদের জীবনের দিনগুলোকে এমনভাবে এলোমেলো করে দিয়ে কোন মহাপ্রভু কতটুকু বাজি জিতলেন তার হিসেব আমরা সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষরা পাব না। তবে আমাদের রক্তে জয়তিলক কেটে আজ অনেকেই স্ফীত হয়ে উঠেছে তা চোখের সামনেই দেখছি। কিন্তু গরিব হিন্দু বা মুসলমান কতটুকু লাভবান হয়েছেন এই হানাহানিতে?
আমাদের গ্রামের নাম ‘বারোঘর’। এ নামের উৎপত্তি হল কোথা থেকে তার স্পষ্ট কোনো ইতিহাস না থাকলেও যতদূর জানা যায়, পূর্বকালে বারোজন প্রসিদ্ধ মহাপন্ডিতের বাস ছিল এই গ্রামটিতে। মুক্তাগাছা, গৌরীপুর, রামগোপালপুর, কালীপুর প্রভৃতি ময়মনসিং জেলার নামকরা জমিদারদের টোলের পন্ডিত ছিলেন এই বারোজন ব্রাহ্মণ। তাঁদের পান্ডিত্যে নেত্রকোণা মহকুমা এই গ্রামের সম্মান বৃদ্ধি করেছে নানাদিক থেকে। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সকলেই তাই আমাদের গ্রামটিকে সম্মান এবং সমীহ করে চলত। এই বারোজন ব্রাহ্মণকে কেন্দ্র করেই ‘বারোঘর’ গ্রামের সূচনা। পাশ্চাত্য শিক্ষা যখন অন্য সব গ্রামকে কবলিত করেছে, তখনও এই গ্রাম সযত্নে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে এড়িয়ে চলে আসছিল, কিন্তু কালের কুটিল গতিতে সবই একদিন ভেসে গেল। টোল ছেড়ে ছেলেরা স্কুল-কলেজে ঢুকতে লাগল। ছোটোবেলায় দেখেছি কত দূর দূর থেকে লোক আসত আমাদের গ্রামে বিধান বা ব্যবস্থা নেবার জন্যে–কেউ শ্রাদ্ধের, কেউ বিয়ের, আর কেউ বা প্রায়শ্চিত্তের।
‘বাবোঘর’ প্রাইমারি স্কুল, কাশতলা মাইনর স্কুল’ এ দুটি বিদ্যায়তন এ অঞ্চলে বহু প্রাচীন। বৃদ্ধদের মুখে শুনেছি এখানে পড়েনি এমন বড়ো কাউকে পাওয়া যাবে না। প্রায় সকলের বাপ-ঠাকুরদাই এই স্কুল দুটির ছাত্র ছিলেন। দূর গ্রাম থেকে খালি গায়ে খালি পায়ে হেঁটে ছেলেরা আসত বিদ্যার্জন করতে। শিক্ষক ছিলেন মাত্র দুজন। বেড়াছাড়া, চালা-দেওয়া ঘরের মাঝখানে বসতেন মাস্টারমশাই আর তাঁকে বেষ্টন করে বসত ছাত্রবৃন্দ। স্কুলের চারপাশের ঝোঁপঝাড়ের মধ্যে সাদা হয়ে ফুটে রয়েছে গন্ধহীন কত শেতকড়ি ফুল। পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় স্কুলকে কুঞ্জবন বলে ভুল হলেও কোনো দোষ দেখি না! ভাবতেও বুক ফেটে যায় আজ যে, সেই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা গ্রামটির কী কদর্য রূপই না হয়েছে। সেই নীরব কুঞ্জ আজ জঙ্গলাকীর্ণ, গ্রামবাসী দেশছাড়া, নির্জন নিভৃত গ্রামে সকাল-সন্ধে আজ কেবলি শেয়াল ডাকছে। সাপের ভয়ও নাকি খুব বেড়ে গেছে শুনেছি। কালসাপের ছোবলে লখিন্দরের মতো আমরাও মৃত্যুপথযাত্রী, এ ছোবল থেকে মুক্তি দেবার মতো শক্ত জবরদস্ত রোজার সন্ধান পাইনি। লখিন্দর শেষে প্রাণ পেয়েছিলেন, সম্পত্তি পেয়েছিলেন বলে জানি, কিন্তু আমরাও কি পাব সেসব কোনোদিন? বিষে বিষে নীলকণ্ঠ হয়ে উঠেছি! বিষয়ের পন্থা কী তা আমাদের অজানা থেকে যাবে সারাজীবন? ভবিষ্যৎ বংশধরেরা আমাদের মূর্খতাকে ক্ষমা করবে কী করে, জানি না।
জলে ছলছল চোখ-দুটির সামনে কেবলি ভেসে উঠছে গ্রাম্য স্কুলের শান্ত মধুর চিত্র। আমগাছের ছায়ায় জটলা করছে ছেলের দল, কেউ বা ঢিল দিয়ে কচি আম পাড়তেই ব্যস্ত, হঠাৎ শোরগোল উঠল–”হেডমাস্টার আসছেন রে।’ মুহূর্তে সমস্ত লোভ সংবরণ করে ছেলেরা দৌড় মারল যে যেদিকে পারে। হেডমাস্টারমশাইকে বড়ো ভয় করত ছেলেরা তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্য–ইংরেজিতে তাঁর জ্ঞানও ছিল অসাধারণ। চমৎকার ইংরেজি বলতে পারতেন তিনি। শুধু বরদাবাবুই নন, এ স্কুলের কথা উঠলেই মনে পড়ে গঙ্গাচরণবাবু, উমেশবাবু প্রভৃতির সহৃদয়তার কথা। পাশের গ্রাম বারহাট্টায় উচ্চ ইংরেজি স্কুল হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের গ্রামের স্কুলের আকর্ষণ কমে আসে। কোনোরকমে আরও কিছুদিন চলার পর এতদিনের ঐতিহ্যময় স্কুলটি শূন্যে মিলিয়ে গেল।
বারহাট্টা স্কুলের নামের সঙ্গে আর দুটি নাম জড়িয়ে রয়েছে। তাঁরা হচ্ছেন তার প্রতিষ্ঠাতা মোহিনী গুণ আর শশী বাগচি। বহুশক্তিক্ষয় করে, অর্থব্যয় করে স্কুলের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন তাঁরা। কতবার কত দুর্যোগ এসে স্কুলটিকে বিপন্ন করে তুলেও উঠিয়ে দিতে পারেনি, জানি না আজ স্কুলের প্রাণশক্তি আর কতটুকু অবশিষ্ট আছে। একদিনের ভয়াবহ ঘটনা মনে পড়ে। রাত্রে হঠাৎ শত্রুপক্ষীয় কেউ স্কুলের খোঁড়া ঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়–সে দৃশ্য ভাবলে আজকে এতদূরে থেকেও রোমাঞ্চ লাগে। শিক্ষাসংস্কৃতির মুখাগ্নি করেই তো দেশব্যাপী সূত্রপাত হয় বর্বরোচিত হত্যাকান্ডের! সুকুমার বৃত্তির এই নির্বাসন কেমন করে কার উস্কানিতে সম্ভবপর হল তা জেনেও আমরা মিলিতভাবে প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হইনি সেই অশুভ শক্তিকে।
বিদ্যালয়-ভবনে ওই অগ্নিকান্ডের স্মৃতি কতৃপক্ষকে দাবিয়ে রাখতে পারেনি,–জিদ এবং উদ্যম আরও যেন বেড়ে গিয়েছিল এরপর থেকে। আমাদের গ্রামে শিক্ষার প্রচলন দেরিতে শুরু হলেও তার অগ্রগতি হয়েছিল খুব দ্রুত। সংস্কারাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রামে মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজন কেউ অনুভব করেননি প্রথমে, কিন্তু হঠাৎ অমূল্যদা, সুধীরকাকা প্রভৃতির চেষ্টায় মেয়েদের স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব হল। তখন গ্রামে সে কী প্রাণস্পন্দন! ছোটো ছোটো বঞ্চিত মেয়েদের মুখে সে কী অফুরন্ত হাসি! মহকুমা হাকিম স্বয়ং এসে স্কুল উদ্বোধন করলেন। আর এসেছিলেন শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। গ্রামের মেয়েরা শিক্ষা ও প্রেরণা পেলে কত ভালো কাজ করতে পারে, তার কথা সেদিনের সভায় অনেকেই শুনিয়েছিলেন। গ্রামের লোকেরা সমস্ত গ্রামটিকে ঝকঝকে তকতকে করে ভদ্রমন্ডলীর প্রশংসার্জনে সক্ষম হয়েছিল। আজ আর সে স্কুলে ছাত্রী নেই, তবুও পূর্ব সুখস্মৃতি মুছে যায়নি মন থেকে।
বিপিনের রামায়ণগান আর হেমুর ঢপযাত্রার কথা আমাদের গ্রামের প্রত্যেকটি লোকের মনে থাকার কথা। এদের অনুষ্ঠান সবচেয়ে বড় আকর্ষণীয় ছিল গ্রামে। সমস্ত ময়মনসিংহ জেলায় বিপিনের মতো গাইয়ে ছিল না বললেই হয়। সেই সত্তর বছরের বুড়ো কী করে হনুমানের ভূমিকায় অত জোরে লাফ দিত তা আজ ভেবে পাই না। একাই সব ভূমিকায় অভিনয় করার তার ছিল বিশেষত্ব–একবার হনুমান হয়ে ল্যাজ নাড়িয়ে আকাশ লক্ষ করে লাফ দেয়, পরক্ষণেই প্রভু রাম হয়ে তীরধনুক নিয়ে করে সমুদ্রশাসন, আবার পরমুহূর্তেই মিত্র বিভীষণ সেজে গান শোনায় বিপিন। তার গান লোকদের একাধারে হাসাত এবং কাঁদাত। পাতাল-অধিপতি দুষ্ট মহীরাবণ নানা ছদ্মবেশে প্রতারণা করতে আসছে হনুমানকে, কিন্তু তীক্ষ্ণবুদ্ধি হনুমানের কাছে বারবার মহীরাবণ হচ্ছে পরাজিত। অবশেষে বিভীষণের রূপ ধরে সে দুর্গে ঢুকে রাম-লক্ষ্মণকে চুরি করে পালায় পাতালে। হনুমান প্রকৃত বিভীষণের গলা ল্যাজে বেঁধে চিৎকার করে বলে—’ওরে পাপিষ্ঠ রাক্ষস, তুই মোর প্রভুরে করেছিস হরণ! মারি তোয় দূরিব প্রাণের জ্বালা!’ আবার পরক্ষণেই বিলাপবিধুর সুর শোনা যায়–’ওরে ভক্ত হনুমান, এরই জন্যে কি দাদার সাথে করেছিস কলহ?’ এসব অভিনয় দেখে এমন কোনো শ্রোতা থাকত না, যারা শুকনো চোখে বসে থাকতে পারত। বিশ্বাসঘাতক মহীরাবণ আজ সারাপৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, বিপিনের মতো গলাধাক্কা দিয়ে আজ তাদের কে সরিয়ে দেবে? কে তাদের স্বরূপ প্রকাশ করে সমস্ত মানুষকে সাবধান করে দেবে বিপিনের মতো? সিনেমা-থিয়েটারের চেয়েও আকর্ষণীয় সেই গ্রাম্য যাত্রা শোনা আর কি কোনোদিন ভাগ্যে জুটবে–যেতে পারব কোনোদিন ছেড়ে-আসা গ্রামে, বিপিনের আসরে!
মনে পড়ে যোগেন্দ্রকে–পাগল ভবঘুরে হলেও আজ তাকেই বেশি করে মনে পড়ছে। ব্রাহ্মণ-সন্তান হয়েও ঘুরে বেড়াত চাষিপল্লির প্রতিটি ঘরে। তাদের সুখদুঃখের খবর নিত, তামাক খেত, গল্প করত প্রাণভরে। এই অমার্জনীয় অপরাধের জন্যে বেচারিকে মাতব্বররা একঘরে করে গ্রামছাড়া করেছিলেন।
আর একটা ঘটনা ভাবলে এখনও হাসি চাপতে পারা যায় না।
যোগেন্দ্রের পাশের বাড়িতে থাকত প্রসন্ন। একদিন প্রসন্ন চুপিচুপি যোগেন্দ্রের খিড়কি বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ কাটছে, টের পেয়ে যোগেন্দ্র বাধা দিতে গেল, ফলে শুরু হল হাতাহাতি। রাগ সামলাতে না পেরে প্রসন্ন হাতের কুড়োলের হাতলি দিয়ে আঘাত করল যোগেন্দ্রের মাথায়, যোগেন্দ্রও ছাড়বার পাত্র নয়, সেও বসিয়ে দিল প্রসন্নের পায়ে এক লাঠি। মামলা হল প্রসন্নের অভিযোগে। নেত্রকোণায় তখন মুন্সেফ ছিলেন বিখ্যাত সাহিত্যিক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। হাকিমের প্রশ্নের উত্তরে আসামি জবাব দেয়–”হুজুর, ব্যাপারটা এই যে, প্রসন্নবাবু আমার দাদা হন। দাদা হিসেবে তিনি আমাকে আশীর্বাদ করতে পারেন সে কথা এক-শো বার স্বীকার করব। তাই দাদা যখন ভাইয়ের মাথায় অমানুষিকভাবে আশীর্বাদ করলেন তখন বাধ্য হয়েই আমাকেও দাদার শ্রীচরণে প্রণাম জানাতে হল। তবে সাধারণ নিয়মানুযায়ী প্রণামটা আগে হওয়াই উচিত ছিল! মনে পড়ে সে-দিন সমস্ত কোর্ট ঝলমলিয়ে উঠেছিল হাসির গমকে।
আমাদের গ্রামটি ছিল হিন্দুপ্রধান। দুরে মুসলমানপাড়া থেকে তারা আসত ধান কিনতে, কিংবা দেনাপাওনার ব্যাপার নিয়ে। কিন্তু যার সঙ্গে আন্তরিকতা ছিল সারা গ্রামের সে হচ্ছে দাসু ফকির। মুসলমান হয়েও হিন্দুর আচার-ব্যবহারে সে শ্রদ্ধাশীল। তন্ত্রমন্ত্র, ভূত-তাড়ানো ইত্যাদি ব্যাপারে তার হাত ছিল পাকা। তেলপড়া, জলপড়া দিতে নিত্যই তাকে আসতে হত আমাদের গ্রামে। তার দেওয়া মাদুলি আমার শরীরেও শোভাবর্ধন করছে। ফকিরের অবাধ যাতায়াত ছিল সব বাড়িতেই। ছেলে কেমন আছে গো’ বলে ঢুকত সে বাড়ির মধ্যে–তারপর চলত তুকতাকের মহড়া! বিড়বিড় করে মন্ত্রপাঠ করে ফুঁ দিয়েই সে রোগ তাড়াত; দেখে অবাক হয়ে যেতাম। তার কান্ডকারখানা আজকেও বিস্ময় জাগায়। জিন গাছের ডাল ভেঙে নিয়ে সে আমাদের বাড়িমুখো এগুতেই তাকে সেবার প্রশ্ন করেছিলাম—’এ বছরটা কেমন যাবে রে দাসু ফকির?’ অসংকোচে গম্ভীর হয়ে সে জবাব দিয়েছিল—’খুব দুর্বছর! তুফান হবে, কলেরা-বসন্তে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। মহামারি লাগবে দেখো কীরকম জোর।‘ অক্ষরে অক্ষরে ফলে যায়। সেবারেই গাঁ উজাড় হয়ে গেল–বাংলাদেশে মানুষ পশুর পর্যায়ে নেমে এসে মৃত্যু-বন্যায় ভেসে গেল! তখন ভাবিনি এমনভাবে দেশ ভাগ হয়ে দাসু ফকিরের কথা সত্যি প্রমাণিত হবে।
গ্রামের সবচেয়ে আনন্দের দিন ছিল দুটি–একটি শ্রাবণী সংক্রান্তি, অপরটি চৈত্র সংক্রান্তি। সাপের ভয়ে পূর্ববাংলার গ্রামবাসীরা সর্বদাই ভীত। প্রতিবছর সাপের কামড়ে মারা যায় বহুলোক। তাই মা মনসাকে তুষ্ট করার জন্যেই প্রতিবাড়িতে ব্যবস্থা হয় মনসা পুজোর। সামর্থ্যানুযায়ী পুজোর আয়োজন। হাঁস, পাঁঠা, আর কবুতর বলি থেকে কুমড়ো পর্যন্ত বলি দেওয়া হত। অতিপ্রত্যূষেই ছেলেরা বিছানা ছেড়ে জমা হত খালের ধারে। সূর্যকিরণে খালের জলের ঢেউ চিকচিক করছে, দূরে দেখা যাচ্ছে ছোটো ছোটো নৌকা। ছেলে-বুড়ো খালের জলে ডুব দেয়, ডুব দিয়ে উঠে বসে। হাত চালিয়ে শাপলা ফুল তুলে নৌকো নেয় ভরে। ফিরে এসে সব বাড়িতে বাড়িতে সে ফুল ভাগ করে দেয় তারা। পুজোর ফুলের জন্যে ভাবতে হয় না কাউকেই। যে বাড়িতে পুজো নেই তারাও ফুলের ভাগ থেকে বাদ পড়ে না। শাঁখ, কাঁসর, ঘণ্টা বাজিয়ে আরম্ভ হয় মনসা পুজো। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি। ছেলেরা মহা উৎসাহে বাজনার মহড়া দেয়, কাউকে ডাকার প্রয়োজন নেই, মান-সম্মানের কোনো বালাই নেই, সকলেই আসে স্বেচ্ছায়। ছেলেদের হাতে দেওয়া হয় না। এরই মধ্যে মিশে রয়েছে আন্তরিকতার সুর। চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষ্যেও সেই একই মিলনের সুর বেজে উঠত পল্লিজীবনে। কিন্তু আজ আর সে সুর নেই, বেসুরো জীবন অনির্দিষ্টের পথে এগিয়ে চলেছে।
অদূরে কংস নদীর কূলে কূলে কত প্রান্তর, কত অরণ্য–মাঝে মাঝে এক-একটি পল্লি প্রতিমা। নদীর তীরে নিত্য আসে তরুণ রাখালেরা গোরু-মোষ চরাতে। পাশে অরণ্য, ধু-ধু প্রান্তর–ভয় লাগে তাদের মনে। অজ্ঞাত প্রিয় বান্ধবীর গাওয়া গান সুর ধরে গাইত তারা,
মইষ রাখো মইষাল বন্ধুরে কংস নদীর কূলে,
(অরে) অরণ্য মইষে খাইব তোরে বাইন্ধা নিব মোরে।
নির্জনতা ভেঙে খানখান হয়ে যেত রাখালের সেই গানে, ভয়ডর সব দূর হয়ে যেত মন থেকে। বন্ধুর জন্যে কী আকুলতাই না ফুটে উঠত সে গানে, সে সুরে। আজ আমরা যারা দেশছাড়া হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছি, তাদের জন্যে কোনো প্রতিবেশী বন্ধু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেছে জানতে পারলে এ দুঃখের মধ্যেও কত শান্তি পাওয়া যেত।
কত কথা, কত ব্যথা আজ মনকে ভারাক্রান্ত করছে–সমস্ত আন্তরিকতা, সহৃদয়তার এমন সলিলসমাধি হবে কে জানত! শ্রীদাম ধোপার অকালমৃত্যু বা অনিলদার আকস্মিক জীবনাবসান সমস্ত গ্রামের চোখে জল এনেছিল একদিন, আর আজ সমস্ত বাঙালি জাতির অপমৃত্যুতে কারও ভ্রূক্ষেপই নেই দেখে মন অবশ হয়ে আসছে।
.
কালীহাতী
প্রভাতের আরক্ত তপন পুব আকাশে উঁকি দেন–ধরণীর মুখের উপর হতে অন্ধকারের অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হয়ে যায়। তন্দ্রাচ্ছন্ন মহানগরীর বুকে জাগরণের সাড়া পড়ে। শুরু হয় কর্মক্লান্ত জীবনের পথে দিবসের পথচলা। ছন্নছাড়া অভিশপ্ত মানুষের দল ভিড় করে রাস্তার মধ্যে খুঁজে বেড়ায় অন্তহীন তমিস্রার মাঝে সমুখের উদীয়মান পথরেখা।
কোলাহলমুখরিত নগরীর বুকে আমারও আত্মকেন্দ্রিক জীবনের শুরু হয় লক্ষ্যহীন পদক্ষেপে। প্রভাতের নবারুণ আমার জীবনে আনে না কোনো নতুন আশার আলো, শোনায় না কোনো উদ্দীপনার অগ্নিমন্ত্র। সে যে পথভ্রষ্ট জীবনপথে ছন্দহীন পথচলা। কর্মহীন বেকার জীবনে মনের খোরাক নিঃশেষ হয়ে আসে–জীবনীশক্তিও শেষ হতে চায় বুঝি! সীমাহীন দুঃখের মধ্যেও মনের কোণে ঝংকার তোলে শুধু অতীতের গর্ভে বিলীয়মান দিনগুলোর মধুময় স্মৃতি। পশ্চাতের অতিক্রান্ত পথের বুকে ছোটো-বড়ো পদচিহ্নগুলো আমার মিশে আছে সুদূর অতীতের পাতায় পাতায়–ফেলে বুকের পরে। তারা টানে–আমায় নিরন্তরই টানে।
লোকে বলে—’জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।‘ স্বর্গের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ নই আমি। কিন্তু স্বর্গাদপি গরীয়সী পল্লিজননীর স্নেহের আস্বাদ পেয়েছি–খুব বেশি করেই পেয়েছি। তাই তাকে ভুলতে পারি না কল্পনাও করতে পারি না ভুলে যাবার। ভাবতে গিয়ে হৃদয় ব্যথাতুর হয়ে ওঠে–পল্লিমায়ের কোল হতে বিচ্যুত হয়ে যাবার কথায়। বেদনাবিধুর হৃদয়ের বেলায় বেলায় ‘আছাড়ি বিছাড়ি’ পড়ে শত সহস্র বিক্ষুব্ধ তরঙ্গরাশি।
লক্ষ লক্ষ গ্রামে গাঁথা এই বঙ্গভূমি। এরই শতকরা নিরানব্বইটা গ্রামের মতো অতি সাধারণ–অতিনগণ্য আমার পল্লিজননী। ইতিহাসের স্থায়ী আসন করে নেবার মতো মূলধন নেই তার–পারেনি কোনো মহামানবের জন্ম দিয়ে প্রসিদ্ধি অর্জন করতে। তবু তাকে ভালোবাসি–শত দোষত্রুটি, শত দীনতা সত্ত্বেও প্রাণের চাইতে ভালোবাসি আমার পল্লিজননীকে। এর আম্রবীথি-ঘেরা ঝিঁঝি ডাকা ধূলিধূসর পথের প্রত্যেকটি ধূলিকণা আমার পরিচিত, আমার অতীত স্মৃতি রয়েছে বিজড়িত হয়ে পথিপার্শ্বস্থ প্রত্যেকটি বৃক্ষের পত্রপল্লবে। তাই আমার পল্লিমায়ের কথা স্মরণ করে শতযোজন দূরে বসেও আমার হৃদয় হয়ে ওঠে এক অপূর্ব মধুর রসে আপ্লুত।
গ্রামের দু-দিক বেষ্টন করে রেখেছে সমকোণীভাবে ক্ষীণকায়া একটি ছোটো নদী। নদী। বলা চলে না ঠিক–একটা বড়ো খাল বললেই যথেষ্ট। তবু আমরা একে বলে এসেছি নদী। ফটিকজানি। চৈত্র মাসে জল শুকিয়ে যায় হাঁটুজলের বেশি থাকে না। নদীর নামকরণ নিয়ে মাথা ঘামাইনি, ফটিকের মতো স্বচ্ছ জলের অভাবে অনুযোগও করিনি কোনোদিন। বর্ষার দিনে দু-কূলপ্লাবী স্রোতস্বিনীর কর্দমাক্ত জলের বুকেই ঝাঁপিয়েছি ঘণ্টার পর ঘণ্টা। গা ভাসিয়ে দিয়ে ভেসে উঠেছি গিয়ে শ্মশানঘাটে, কালীবাড়িতে, কোনোদিন বা খেয়াঘাটে।
উত্তরপাড়ার সেনেদের বাঁধানো ঘাটে দুপুরবেলায় ভিড় জমত পাড়ার মেয়েদের। সত্তর বছরের বুড়ি ঠাকুমা থেকে শুরু করে পাঁচ বছরের নাতিনাতনি খেদি, পটলা, খুকি পর্যন্ত। স্নান করতে করতে চলত কত হাসি, কত গল্প, কত রং-তামাশা। মায়েরা বাচ্চাদের ধরে ধরে জোর করে সাবান মাখাতে বসত–আর সেই সব ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদের সমবেত কান্নায় ঘাটের আকাশ-বাতাস উঠত মুখরিত হয়ে। তারই মধ্যে যত রাজ্যের চলত গল্প। ‘অ দিদি, কী রান্না হল আজ?’ ‘কী যে করি ভাই, ছোটো খুকিটার ক-দিন থেকে জ্বর হচ্ছে। ছাড়ছে না কিছুতেই।’ ‘ও মা! তাই নাকি! পোড়ামুখো কী আবার ষাট বছরে বিয়ে করতে যাচ্ছে নাকি?’ এমনি আরও কত শত কথা।
বর্ষায় স্ফীত ফটিকজানি দুকূল ভাসিয়ে দিত মাঝে মাঝে। মনে পড়ে কী অপরূপ পরিবেশের সৃষ্টি করত জ্যোৎস্নাস্নাত তটিনীর অতুলনীয় রূপমাধুরী। অপূর্ব মোহাবেশের বিস্তার করত ফটিকজানির সেই নৈশ রূপমাধুর্য। কত চাঁদিনি রাতে ডিঙি ভাসিয়ে দিয়েছি আমরা ফটিকজানির সেই শান্ত সমাহিত বুকের পরে! বাঁশির সুরে ভরে দিয়েছি নিশীথ রাত্রির আকাশ-বাতাস। জ্যোৎস্নাবিধৌত পল্লির অপরূপ রূপের তুলনা নেই কোথাও। রূপকথায় শোনা স্বপনপুরীর রূপমাধুর্যও হার মানে তার কাছে। গাঁয়ের মধ্যে আমরা কয়েকজন ছিলাম ডানপিটে। কত নিশুতি রাতে দলবেঁধে আমরা মৎস্যশিকারের উদ্দেশ্যে অভিযান করেছি খ্যাতনামা সাতবিলের দিকে। কত কিংবদন্তি প্রচলিত ছিল এই বিলের নামে! অভিশপ্ত প্রেতাত্মা, অশরীরী কত আত্মা নাকি ঘুরে বেড়ায় সাতবিলের ওপর দিয়ে। প্রত্যক্ষদর্শী কত মৎস্যশিকারির মুখে শুনেছি এসব কাহিনি–অবাক হয়ে গিয়েছি রামনামের অত্যাশ্চর্য মহিমায়–তখন বিশ্বাস করেছি তাদের সে সমস্ত অতিরঞ্জিত কল্পিত ভয়-কাহিনি। মনে পড়ে রামকান্ত মাঝির কথা। আমাদের প্রজা ছিল সে। আমাদের বাড়ির পাশেই বাড়ি। কত রাত্রি জেগে যে রামকান্তদার কাছে বসে এই সমস্ত মৎস্যলোভী অশরীরীদের গল্প শুনেছি তার হিসেব নেই। জাল বুনতে বুনতে গল্প বলত রামকান্তদা। তার নিজস্ব অভিজ্ঞতা নাকি সেসব। আমার শিশুমনের ওপর সে কাহিনিগুলো বিস্তার করত এক অপূর্ব মায়াজাল। তারপর বড়া হয়ে কতদিন অভিযান করেছি অপদেবতা অধ্যুষিত সাতবিলে–যোগীমারা দহের স্থির স্তব্ধ জলরাশির ওপর দিয়ে। কিন্তু কোনোদিনই সৌভাগ্য হল না সেই অশরীরী আত্মাদের দর্শন লাভের; কোনো অবগুণ্ঠনবতী রমণী কোনোদিন আমার কাছে এসে আনুনাসিক সুরে প্রার্থনা করল না মাছ। মধুর সে সমস্ত দিনগুলোর স্মৃতি কী করে ভুলব?
গ্রামের প্রধান অংশ মুনশিপাড়া। বনেদি জমিদার এ পাড়ার প্রধানরা। বাড়িগুলো এদের পড়ে আছে আজ পরিত্যক্ত মরুভূমির মতো। আগাছার ঝোঁপঝাড়ে ভরে আছে গ্রামের রাস্তাঘাট। দিনের বেলায়ই ভয় হয় পথ চলতে। এমনটি কিন্তু ছিল না কোনোদিন।
মুনশিদের উদ্যানের ভগ্নাবশেষের পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়েই পৌঁছোতে হয় ভাঙা-পুলের বুকে। সাহাপাড়ার মধ্যে অবস্থিত সে পুলটি। সংকীর্ণ একটি খালের মধ্য দিয়ে গাঙের জলরাশি এসে আছাড়ি-বিছাড়ি পড়ে ওই পুলের তলদেশে। শত শত আবর্তের সৃষ্টি করে বয়ে যায় বাঁশঝাড়ে রচিত তোরণের মধ্য দিয়ে কর্মকার পাড়ার দিকে। আপরাহের পড়ন্ত রোদে গাঁয়ের ছেলেদের আড্ডা বসত পুলের ওপর–গল্পে, উচ্চহাসিতে, হইচইতে কেটে যেত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। পৃথিবীর বুকে নেমে আসত ক্রমে রাত্রির যবনিকা।
কামারপাড়ার বাঁশঝাড়ে ঢাকা গতিপথে গিয়ে খালটি মোড় ফিরেছে পদ্মিনী বুড়ির বাড়ির কাছে। ফিরে বইতে শুরু করেছে সাতুটিয়ার পুলের দিকে। মনে পড়ে পদ্মিনী বুড়ির কথা। কতদিন স্কুল পালিয়ে হানা দিয়েছি বুড়ির কাশীর কুলগাছে-কাঁচা-মিঠে আম গাছে। কাংস্যকন্ঠ সপ্তমে চড়িয়ে মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে দৌড়ে এসেছে বুড়ি-ভগবানের কাছে আবেদন করেছে আমাদের চোদ্দো পুরুষের কায়েমি নরকবাসের জন্যে। পঞ্চাশ সালে গলেপচে মারা গেল পদ্মিনী বুড়ি অশেষ কষ্ট পেয়ে।
মনে পড়ে আজ হেমন্তের অপরাহ্ন পাড়ার ছেলেরা দল বেঁধে বেড়াতে বেরুতাম–সবুজ ঘাসে-ঢাকা মাঠের মধ্য দিয়ে, কোনোদিন মেঘখালির পুলের উদ্দেশ্যে, কোনোদিন বা ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক ধরে অনির্দেশের পানে। দু-ধারে প্রসারিত ছিল শ্যামল বঙ্গজননীর এক নয়নাভিরাম রূপ। মেঘশূন্য নীলাকাশের বুকে লাগত বিদায়ী অরুণের রক্তরাঙা অনুলেপন, ঘাটে-মাঠে-বাটে লাগত অস্তরাগের ছোঁয়া। হারিয়ে গেছে সে দিনগুলো, হারিয়ে গেছে চিরতরে। বন্ধুরাই বা কে কোথায় হারিয়ে গেল জীবনস্রোতের কুটিল আবর্তে, কে বলবে?
গ্রামের একটা প্রধান অংশ কালীবাড়ি। নদীর পাড়ের এই কালীমন্দিরটির কথা শুনে এসেছি ছোটোবেলা থেকেই। জাগ্রতা কালীমাতা। কত অলৌকিক কাহিনির জনশ্রুতি প্রচলিত এই কালীপ্রতিমা সম্বন্ধে। নিশুতি রাতে লালপেড়ে শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াতে নাকি দেখা যেত তাঁকে এই কালীবাড়ির বাঁধানো চত্বরে, কিন্তু চরম দুর্দিনে পাষাণী মা পাষাণীই রয়ে গেল।
বেশিদিনের কথা নয়। বছর খানেক আগেও হরিসংকীর্তনে, যাত্রাগানে এই মন্দির-প্রাঙ্গণ হয়ে উঠত মুখরিত। তাতে কুণ্ঠিত হয়নি মুসলমান জনসাধারণ অংশগ্রহণ করতে। কৃষ্ণবিরহ বিধুরা রাধার দুঃখে তারাও হিন্দু শ্রোতাদের মতো সমানভাবে ফেলেছে সমবেদনার অশ্রুরাশি। পদ্মপুরাণের গানে, কথকতার আসরে, রামায়ণগানে, ত্রৈলোক্যঠাকুরের মেলায় এরাও নিয়েছে মুগ্ধ শ্রোতার অংশ। সমানভাবেই পদ্মপুরাণের গানে তারাও ধুয়া ধরেছে—’বেউলা বলে লখিন্দর, পূর্বকথা স্মরণ করো।’ সানন্দেই তারা গ্রহণ করেছে ত্রৈলোক্যঠাকুরের প্রসাদি গঞ্জিকার অংশ, উচ্চকণ্ঠে গান ধরেছে ভক্তবৃন্দের সঙ্গে—’ত্রৈলোকের মেলারে ভাই যে করিবে হেলা। হস্ত যাবে, পদ যাবে, চোখে বেরুবে ঢেলা।’ হস্তপদ যাওয়ার ভয়েই হোক বা হিন্দু ভাইদের সঙ্গে সম্প্রীতির ফলেই হোক ত্রৈলোক্যঠাকুরকে অবহেলা করেনি তারা। সেই দিনগুলোর কথা আজ মনে হয় বুঝি বা স্বপ্ন। কৈশোরের লীলানিকেতন পল্লিমায়ের বুকে যাদের সাহচর্যে শুরু হয়েছিল আমার জীবনের প্রথম পথচলা–তারা সবাই হারিয়ে গেছে আজ। দুর্যোগময়ী রজনীর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পথমাঝে তারা ছিটকে দূরে গড়িয়ে পড়েছে শত যোজনের ব্যবধানে। কেউ বা তাদের পথ খুঁজে পেয়েছে–কেউ বা পথ খুঁজে মরছে এখনও।
মহেশদাকে মনে পড়ে। একমুখ দাড়িগোঁফে আচ্ছন্ন বেঁটে কালো লোকটি। সদাহাস্যময় মুখ। গ্রামের সব কাজে অগ্রণী। আমাদের সর্বজনীন ‘দাদা’–সকলেরই শ্রদ্ধেয়। বয়স প্রায় ঘাটের কোঠায় পোঁছেছে, দেহের বাঁধন অটুট। কালীবাড়ির বার্ষিক উৎসবে চাঁদা তোলার ব্যাপারে–রাত জেগে পাহারা দেওয়ার জন্যে শখের রক্ষীদলে আমরা মহেশদাকে পেতাম সর্বাগ্রে। খুবই উৎসাহ ছিল বৃদ্ধের। পাহারা দেবার সময় হাঁক দেওয়ার ব্যাপারে জুড়ি ছিল না তাঁর। লাঠিটা সোজা করে তার ওপর ঝুঁকে পড়ে উচ্চকণ্ঠে হাঁক দিতেন মহেশদা-–’বস্তিওয়ালা জা—গো–রে।’ আমরা বলে উঠতাম সব—‘হেঁ—ই–ও।’ এখনও আছেন মহেশদা। তবে নিশুতি রাতে গ্রামের বুকে তাঁর খড়মের শব্দ এখনও ধ্বনিত হয় কি না তা বলতে পারি না।
মনে পড়ে কালবৈশাখীর চৈত্র সংক্রান্তির উৎসব মুখরিত দিনগুলোর কথা। রাত জেগে বাবার চোখ এড়িয়ে দেখতে যেতাম গাজনের মেলা। গ্রামের অশিক্ষিত জনসাধারণ সং সেজে করত কত উৎকট আনন্দের পরিবেশন। অনেক সময় শ্লীলতার সীমা যেত ছাড়িয়ে। তবু কী আনন্দই না পেতাম সেই গ্রাম্য উৎসবের মধ্যে। জিহ্বা ফুটো করে লোহার শিক ঢুকিয়ে উৎসব-প্রাঙ্গণে নৃত্য করত সেইসব পূজারির দল। সারারাত জেগে শ্মশানে গিয়ে দেখতাম কালী হাজরার ‘রাতের ভোগে’র উৎসব। ভোরবেলায় জাগরণক্লিষ্ট দেহে চুপি চুপি বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়তাম বিছানায়। অবাক হয়ে যেতাম ‘কেতু সন্ন্যাসী’র দেহে দেবতার আবির্ভাবের উত্তেজনায়। কী মধুর, কী আনন্দময় মনে হত সে কালটা!
বিজয়া দশমীর কথা ভুলব কী করে? ফটিকজানির বুকে আশপাশের সমস্ত গ্রাম থেকে এসে জড়ো হত প্রতিমা। খেয়াঘাট থেকে শুরু করে এপারের জেলেপাড়ার ঘাট পর্যন্ত ভরে যেত নৌকায়-নৌকায়। তিলধারণের ঠাঁই থাকত না সারানদীতে। নৌকার ওপরে চলত নাচ গান, লাঠিখেলা, সংকীর্তন–আমোদ-উৎসবের হইহুল্লোড়। গাঙের বুক মথিত হয়ে উঠত বাইচ খেলার নৌকার তান্ডব নর্তনে। সে খেলায় বেশির ভাগ অংশই গ্রহণ করত মুসলমানরা।
আশপাশের গ্রামের প্রায় সমস্ত নিরীহ মুসলমান কৃষকদের সঙ্গেই ছিল আমাদের অকৃত্রিম হৃদ্যতা। তারি ভাইয়ের কথা মনে পড়ে। অশীতিপর বৃদ্ধ তারি ভাইয়ের সঙ্গে যখনই দেখা হত, পথের মাঝে জিজ্ঞাসা করতাম–’কেমন আছ তারি ভাই?’ ভালো করে চোখে দেখত না সে। শব্দ লক্ষ করে কাছে এসে মাথায় মুখে হাত বুলিয়ে ঠাহর করে নিয়ে বলে উঠত-–’কে ভাই? অ, নাতিঠাকুর! এই একরহম আছি। তা তুমি কুঠাই যাবার লাগছ?’ তারপর সেই রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়েই চলত এ গল্প, সে গল্প, তার ছেলেদের দুর্ব্যবহারের কথা। তারপর ঠকঠক করে আবার চলত সে গন্তব্যস্থলের দিকে। এখনও বেঁচে আছে তারি ভাই। গাঁয়ের বুকে এখনও বোধ হয় তার লাঠি ঠকঠক শব্দে ঘুরে বেড়ায়।
আর একজনের কথা মনে পড়ে। ফজু ঢুলি–গ্রামের চৌকিদার। রাস্তায় যখনই দেখা হত তার সঙ্গে আভূমি নত হয়ে বলে উঠত ‘সেলাম কর্তা সেলাম। হেসে জিজ্ঞাসা করতাম –’ভালো আছ?’ সে আবার সেলাম করে বলে উঠত—’আজ্ঞে, খোদায় রাখছে ভালো।’ মনে পড়ে কত রাত্রে ঘুম ভেঙে যেত তার পরিচিত কণ্ঠের আহ্বানে—’কর্তা, জাগেন।’ তারা তো আজও আছে, আজও বোধ হয় ফজু চৌকিদার তার টিমটিমে লণ্ঠনটি নিয়ে ঘুরে বেড়ায় নিশুতি রাত্রে পল্লির রাস্তার রাস্তায়–নিশীথের নিস্তব্ধতা ভেদ করে তার কাংস্যকণ্ঠ ধ্বনিত হয়—’বস্তিওয়ালা জা—গো–রে।’ হঠাৎ ঘুম ভেঙে-যাওয়া এক শিশু হয়তো চিৎকার করে কেঁদে ওঠে কোনো বাড়িতে। উৎকট চিৎকারে বিরক্ত হয়ে একটা নিশাচর পাখি হয়তো উড়ে যায় এগাছ থেকে ওগাছে ডানার ঝটপটানিতে অনধিকার প্রবেশের প্রতিবাদ জানিয়ে।
এমনি আরও কত শত পরিচিত মুখ মনের দুয়ারে উঁকি মারে। এরা যে ছিল আমার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত।
এই আমার পল্লিজননী ময়মনসিংহ জেলার টাঙাইল মহকুমার কালীহাতী গ্রাম। পিতৃপিতামহের ভস্মাবশেষ মিশে রয়েছে ধূলিধূসর এ গাঁয়েরই মাটির সঙ্গে। সপ্তপুরুষ আমার এরই বুকের ওপর হয়েছে লালিত পালিত।
তাই তো এখনও ভালোবাসি, শত মাইল দূরে বসেও স্মরণ করি আমার সেই গ্রামকে, আমার সেই পল্লিজননীকে। পেছনে ফেলে-আসা সেই ধূলিধূসরিত আম্রবীথি-ঘেরা ছায়াসুশীতল বনপথকে কী করে ভুলব? সে পথের বুকে আমার পিতৃপিতামহের চরণধূলি মিশে আছে অণুতে অণুতে। সমুখের পথে পাই না কোনো আলোর হাতছানি, তাই তো পেছনের অতিক্রান্ত পথ আমায় ডাকে–কেবলই ডাকে। অমোঘ আকর্ষণ সেই আহ্বানের। স্বর্গাদপি গরীয়সী পল্লিমায়ের আকুল আহ্বান প্রতিহত হয়ে ফেরে ব্যবধানের প্রাচীন গাত্রে–ফিরে যায় ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে। ভুলতে পারি না তাকে-–ভুলতে পারবও না কোনোদিন! মনে পড়ে নিরন্তরই–‘সপ্তপুরুষ যেথায় মানুষ সে মাটি সোনার বাড়া।’
.
সাঁকরাইল
সূর্যাস্তের পানে তাকিয়ে সূর্যোদয়ের কথা ভাবা ছাড়া আর কী করতে পারি আমরা আজ? জীবন থেকে সূর্যালোক চলে গিয়ে সমস্ত কিছুকে অন্ধকার ব্যর্থতার মধ্যে ঢেকে দিয়েছে। তবু আমরা আলোর পূজারি। আলোকের ঝরনাধারায় জীবনকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াসী। জীবন মধুর হোক, আলোকময় হোক, আনন্দময় হোক, এ কে না চায়! মহামরণকে মহাজীবনে পরিণত করার মন্ত্র আপাতত আমরা ভুলে গেলেও হতাশ হব না। জীবন-যৌবন দিয়ে পূর্বসূরিদের মহামিলনের গান আমরা গেয়ে যাব। জানি না আত্মবিস্মৃত মানুষ কবে মিলনের গান গ্রহণ করতে পারবে আবার!
আমার গ্রামের কথা মনে পড়লেই কবি গোবিন্দদাসের ঘর ছাড়ার কথা মনে পড়ে। তাঁর গৃহত্যাগের কবিতা আমাদের জীবনকেও যথাযথ রূপ দিয়েছে যেন,
কোথা বাড়ি, কোথা ঘর কি শুধাও ভাই,
যে দেশে আমার বাড়ি আমি সে দেশের পর–
সত্যি, আমার যে দেশে বাড়ি আমি সে দেশের অনাত্মীয় আজকে। ঘর আছে, গ্রাম আছে, সম্পত্তি আছে অথচ আজ আমি উদবাস্তু। বাস্তুত্যাগীর দুঃখ হৃদয়বান না হলে উপলব্ধি করা
সহজ নয়। দুঃখের সমুদ্র মন্থন করে আজ যে বিষ উঠেছে দেশময়, আমরা তা পান করে নীলকণ্ঠ হয়েছি! অমৃতের পুত্রদের আর সুখ নেই–সুখ, স্বস্তি, শান্তি, প্রেম-ভালোবাসা দেশত্যাগী হয়েছে আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই। চারদিকে কুটিল চক্রান্তের কলুষিত ছবি,–সেই পূর্বদিনের সুখীসচ্ছল মানুষের এবং গ্রামের চিত্র কোথায় অন্তর্হিত হল? মানুষ সুসভ্য হয়েছে শুনতে পাই, কিন্তু এই কি সভ্যতার রূপ? এই জন্যেই কি এত সাধনার প্রয়োজন ঘটেছিল? কোথায় গেল সে প্রাচীন সভ্যতা, সংস্কৃতি, নির্লোভ, নিষ্কলুষতার প্রতীক? কে হরণ করল আমাদের সদগুণগুলো? এই সভ্যতার সংকট থেকে কবে আমরা পরিত্রাণ পাব?
জানি এসব সাময়িক বর্বরতা আমাদের জীবনযাত্রার পথে ছলনা নিয়ে এসে ক্ষণিকের জন্যে আমাদের অগ্রগতি রুদ্ধ করবার চেষ্টা করছে, কিন্তু আমরা সে মোহের জালে ধরা দিলাম কেন? মানুষের আদি নারী-পুরুষ ‘আদম-ইভের সংকট’ কি আবার দেখা দিল বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে? আবার কি শয়তান-কুটিল সাপের ছোবলে মানুষ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনল? কেন এই মতিভ্রম, কেন এই পদস্খলন, কেন এইভাবে মানুষ মহাপ্রস্থানের পথে যাত্রা করছে পরের ধার করা পরামর্শ শুনে?
আমাদের গৈরিকধূসর বৈরাগ্যমন তো কখনো আক্রমণাত্মক ছিল না? লোভের হাতধরা হয়ে কখনো তো সে কোনো নিরীহের প্রাণহরণ করেনি! সামান্য তেঁতুলপাতার ঝোল খেয়েই দিনযাপন করেছেন আমাদের পুর্বপুরুষরা, তবুও প্রতিবেশী রাজার রাজত্বের দিকে লোভাত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেননি–তবে সে স্বর্গ থেকে বিদায় নিতে হল কেন আমাদের? কোন পাপে মানুষ আজ হানাহানিতে মত্ত-ভ্রাতৃরক্তে তার কেন এত তৃপ্তি? কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তো বলে গেছেন, ‘মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে, মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই। গুরুদেব যে মানুষের মধ্যে বাঁচতে চেয়েছিলেন সে মানুষ আজ কোথায়?
বহুদিন মাকে হারিয়েছি কিন্তু আজ হারালাম জননী জন্মভূমিকে। আমার জন্মভূমি আজ আর আমার নয়। তবু তাঁর স্মৃতি মনের মণিকোঠায় জড়িয়ে রয়েছে অচ্ছেদ্য বন্ধনে। মনের ভেতর একটি ছবিই সমস্ত জায়গা জুড়ে আছে–সে ছবি আমার তীর্থভূমির, আমার ছেড়ে আসা গ্রাম সাঁকরাইলের। ময়মনসিংহ জেলার টাঙাইল মহকুমার সাঁকরাইল গ্রামকে আমি কোনোদিন মন থেকে মুছে ফেলতে পারব না। তার সুখ-দুঃখ যে আমার সুখ-দুঃখের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। আমি তার কথা ভুলতে চাইলেও সে আমাকে ভুলবে না– নির্জনস্বাক্ষর উজ্জ্বল হয়ে মনকে সততই প্রশ্নজালে জর্জরিত করবে! শহর থেকে দূরে নির্জন গ্রামখানির এত মোহিনীশক্তি একথা আগে কে জানত?
রাত্রের অসতর্ক মন যখন কল্পনার ডানা বিস্তার করে, তখনই মনে পড়ে যায় আমার গ্রামখানির কথা। শয়নে-স্বপনে, নিদ্রায়-জাগরণে হায় হায় করে ওঠে মন তার কথা চিন্তা করে! ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই হলেও ছেলেরা মাকে ভাগ করতে পারে জানতাম না, আজ দেখছি সব কিছুই সম্ভব মানুষের স্বার্থের কাছে! মাকেও আজ মূর্খ আমরা ভাগের মা করে ছেড়েছি।
যেখানে বারোমাসে তেরো পার্বণ লেগে থাকত সে গ্রাম আজ খাঁ খাঁ করছে মানুষের অভাবে। জঙ্গলে ভরতি হয়ে গেছে উঠোন, লক্ষ্মী আজ গ্রামছাড়া! শুনেছি দিনদুপুরে শেয়াল ডাকে আমাদের বাড়ির মধ্যে–নির্ভীক তাদের পদক্ষেপ, বিস্তৃত তাদের বিচরণভূমি। মনে পড়ছে অতীত আভিজাত্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুরোনো তিনপুরুষের চকমিলানো দালান, পুজোমন্ডপ, দিগন্তপ্রসারী আম-কাঁঠালের বাগান,শান্তির নীড় হাতছানি দিয়ে ডাকলেও সেখানে যাবার উপায় নেই আজ। দুঃখ হয় নিজবাসভূমিতে আজ আমরা পরবাসী হয়ে পড়েছি ভেবে! হাসি পায় ভেবে যে, এই আমরাই বিজয়সিংহের বংশধর–আমরাই হেলায় লঙ্কা জয় করেছিলাম। একটা পাগলামিকে যাদের রোধ করার ক্ষমতা নেই তারা দেশজয়ের গর্ব করে কী করে?
মন ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাচ্ছে অতীত-বর্তমানের হিসেব-নিকেশে, কিন্তু কী পেয়েছি আর কী পাইনি তার হিসেব করতে মন আর রাজি নয়। সে চায় শান্তি, সে চায় আশ্রয়, সে চায় আশপাশে দরদি মানুষ। কোথায় গেল সেসব মানুষ যারা পরার্থে জীবন বিসর্জনেও পরা’খু ছিল না। নিজের স্বার্থ যাদের কাছে বড়ো ছিল না, বড়ো ছিল অন্যের নিরুপদ্রব জীবন, শ্বাপদসংকুল জনপদে তাই আমরা পদে পদে বিপর্যস্ত, প্রাণ বাঁচালেও মান বাঁচানো চলছে না আর!
সিরাজগঞ্জের ঘাটে নেমে যমুনা নদী পাড়ি দিতে হত ফেরিতে, তারপর নৌকাযোগে যেতে হত আমাদের গ্রামে। নদীর বুকে সূর্যোদয়ের জীবন্ত ছবি আজ অন্ধকারেও স্পষ্ট মনে পড়ে। রাঙাবরণ তরুণ তপন আশা নিয়ে আকাশের গায়ে যখন দেখা দিত তখন আমার মাথা আপনি তার পায়ে লুটিয়ে পড়েছে। নদীর জলে পেয়েছি জীবনকে আর যৌবনকে পেয়েছি। সূর্যের মধ্যে,জীবনযৌবন সেদিন আমাকে অশ্বমেধের বেপরোয়া ঘোড়ার গতি জুগিয়েছে –অশান্ত মন লাগামহীন হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে যত্রতত্র। আজও তো সবাই আছে, কিন্তু সে গতি শ্লথ হল কেন? ছ্যাকরাগাড়ির মতো ক্লান্ত পায়ে কতদূর এগিয়ে যেতে পারব? তরুণ সূর্যের আলোতে সেদিন মাঝিমাল্লারাও মনের খুশিতে গান ধরত দাঁড় বাইতে বাইতে। সে ভাটিয়ালি গান দেহতত্ত্বের রসে সঞ্জীবিত ছিল। গানের তালে তালে ছোটো ছোটো ঢেউ কেটে বাড়ির দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা মনে করলে নিজেকে আর সামলাতে পারি না।
সিরাজগঞ্জের হোটেলে ইলিশমাছের ঝোল-ভাত সেদিন যা খেয়েছি তার স্বাদ যেন আজও মুখে অমৃতের মতো রয়েছে লেগে। হোটেলওয়ালাদের দুষ্টুমির কথা মনে পড়লে হাসি পায়। যাত্রীরা খেতে বসলেই তারা স্টিমার ছেড়ে যাচ্ছে বলে ভয় দেখাত, ফলে কম খরচে তাদের হত বেশি লাভ। মনে পড়ছে সেবার এক যাত্রীকে ওই ধরনের ধাপ্পা দিতে গিয়ে হোটেলওয়ালাই ভীষণ জব্দ হয়ে যায়। সে শেষপর্যন্ত হোটেল ফাঁক করে তবে হোটেল ছাড়ে! কত খুঁটিনাটি কথাই মনের মধ্যে উঁকি দিচ্ছে আজ।
দেশে পৌঁছে ছোটো ভাইবোনদের সঙ্গে পুকুরে মাতামাতি করার দৃশ্যটি পর্যন্ত আজ ভুলে থাকবার উপায় নেই। চোখ লাল না হওয়া পর্যন্ত জল থেকে উঠতাম না–কাদাঘোলা জলে পানকৌড়ির মতো ডুব দিয়ে চোর-পুলিশ খেলতাম জলের মধ্যে। সে দিনগুলোই ছিল স্বতন্ত্র ধরনের। আমাদের জীবন থেকে সে দিনগুলি কোথায় গেল?
পুজোর ছুটিতে বাড়ি যাবার তোড়জোড় চলত মাস দুয়েক আগে থেকেই। প্রতিজনের নতুন জামাকাপড় জুতো কিনে বাড়ি যাবার কথা মনে পড়লে আজও রোমাঞ্চ লাগে শরীরে। রাস্তায় ট্রেন-স্টিমারের পথকষ্ট এবং ক্লান্তি নিমেষেই কেটে যেত ঠাকুমা, মা, জেঠিমা, পিসিমা এবং ছোটো ভাইবোনদের মধ্যে গিয়ে হাজির হলে। মাকে ছেড়ে বিদেশে থাকতে পারতাম না বেশিদিন, মাও পারতেন না। বাড়ির স্নেহবঞ্চিত হয়ে সেদিনকার কষ্ট সীমা অতিক্রম করত, কিন্তু আজ? মাকে ছেড়ে, আত্মীয়স্বজন থেকে দূরে সরে এসে, দেশত্যাগী উদবাস্তু হয়ে পথে ঘাটে আজ রাত্রি কাটাই। কোথায় গেল কষ্টবোধ, কোথায় গেল সেই সুখের জীবন? সেদিন যা পারিনি আজ তো বেশ মুখ বুজেই সেসব সহ্য করছি। যাদের দু-বেলা খাবার কষ্ট হবার কথা নয়, তাদেরই উপবাসী থাকতে হচ্ছে আজ নিষ্ঠুর নিয়তির পরিহাসে। আজ অনাহারে অর্ধাহারে টুকরো কাপড়ের স্তূপ ঘাড়ে ফেলে দুয়ারে দুয়ারে ফিরি করতে হচ্ছে অন্নের আশায়। রাস্তার কলের তপ্ত জলে উদরভরতি করে ভিক্ষাবৃত্তি চালিয়ে যেতে হচ্ছে দিনের পর দিন। এই অসহ্য পরিহাসের শেষ কোথায় জানি না, ভবিষ্যতে আরও কী কষ্টের কবলে পড়ব তার খোঁজও রাখি না। মঙ্গলকাব্যে পড়েছি দেবতার কোপে পড়ে মানুষের নাস্তানাবুদ হওয়ার কাহিনি–আমাদের এই কাহিনিও সেই মনগড়া কাহিনির সমগোত্রীয় নয় কি? মঙ্গলকাব্যের কাহিনিশেষে দুঃখীরা ফিরে পেয়েছে সমস্ত হৃত সম্পত্তি ক্রুদ্ধ দেবতাদের তুষ্টিসাধন করে। আমাদের ভবিষ্যৎ কি তার সঙ্গে মিলবে না? কষ্ট করে বেঁচে থাকার পরেও কি সুখের মুখ দেখব না কোনোদিন?
দুঃখের মধ্যেও সুখের স্মৃতি এসে পড়ে মাঝে মাঝে। আমারও মনে পড়ছে আমাদের বাড়ির দুর্গা পুজোর কথা। প্রতিমা সাজানো, প্রতিমায় রং দেওয়া, প্রতিমার আঁচলে জরি-চুমকি লাগানোর কাজে নাইবার-খাবার সময় থাকত না আমার! মহাব্যস্ততা এবং হইচই-এর মধ্যে কাটত দিনগুলো। লক্ষ করেছিলাম প্রতিমার রং লাগানোর সময় গ্রামের হিন্দু-মুসলমানেরা আসত আগ্রহভরে হাত ধরাধরি করে। মুসলমান বলে আমার গ্রামবাসীরা দূরে সরে থাকত না কখনো। রং দেওয়ার ব্যাপারে তারাও মাঝে মাঝে পরামর্শ দিত পটুয়াদের! কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল সাধারণ মানুষ ধরতে পারল না, কিন্তু যখন বুঝতে পারল তখন সর্বনাশসাধন হয়ে গেছে। তখন মনের অপমৃত্যু ঘটেছে, বনস্পতিঘন বৃহদারণ্য দাবানল জ্বলছে দাউ দাউ করে।
অনেকের বাড়িতে বেলবরণ হত পুজোর একমাস আগে, কিন্তু আমাদের বাড়িতে হত। ষষ্ঠীর দিন সন্ধেবেলায়। বাজনদাররা এসে হইচই করে ঢাকঢোল সানাই কাঁসির বাজনায় মাতিয়ে তুলত চারদিক, বাজনার সঙ্গে চলত নাচ। হইহুল্লোড়ে কানের পর্দা ফাটবার উপক্রম হত। আমরা সবাই ছুটে এসে বাজনার তালে তালে কোমর দুলিয়ে আরম্ভ করে দিতাম খেয়াল নৃত্য–সেদিনকার নাচ যে প্রলয় নৃত্যের বেশে জীবনে দেখা দেবে তা কে ভেবেছিল? নাচের মুদ্রা ঠিক কি না জানি না, তবে সে উদ্দাম নাচ যে স্বতঃস্ফুর্ত ছিল সে কথা হলপ করেই বলতে পারি। গুরুজনরা পুজোমন্ডপে সমবেত হতেন। কতরকম বাজি যে পোড়ানো হত তার সীমাসংখ্যা ছিল না। এইরকম ধুমধামের মধ্যে মা দুর্গা উঠতেন বেদিতে।
পরদিন সপ্তমী পুজোর প্রত্যূষেই সানাই-এর সুর দিত ঘুম ভাঙিয়ে, চোখ মেলে দেখতাম খুশির প্রস্রবণ। চারদিকে প্রাণের মেলা,-আনন্দের ঢেউ। সেই ভোরবেলাতেই বেরিয়ে পড়তাম শিউলিফুল আহরণে। ফুল কুড়োনোর মধ্যেও ছিল তীব্র প্রতিযোগিতা–কার সঞ্চয় কত বেশি তার হিসেব নিয়ে কথা কাটাকাটি থেকে সময় সময় যে হুটোপুটির পর্যায়ে পৌঁছোত না তাই বা বলি কী করে! কে পদ্মফুল পেল, কে পেল না, কার ডালায় রকমারি ফুল কত বেশি তা দেখে বাবা-মা পয়সা দিতেন পুরস্কার হিসেবে। সে পয়সা সামান্য হোক তবু তা আমাদের শিশুমনের কাছে ছিল অমূল্য।
মহাস্নানের পর মহাসপ্তমী পুজো হত শুরু। পুরোহিত ঠাকুর চিৎকার করে ডাক দিতেন–‘এসো তোমরা সব্বাই, অঞ্জলি দেবে এসো।’ অঞ্জলি দেওয়ার পর প্রসাদ গ্রহণের পালা। সেদিন দশপ্রহরণধারিণী, সিদ্ধিদাতা গণেশজননী, শত্ৰুবিজয়িনী মা দুর্গার ভক্তিভরেই অঞ্জলি দিয়েছি, প্রণাম করে শত্ৰুদলনের মন্ত্র চেয়ে নিয়েছিলাম ভক্তিভরে, কিন্তু তিনি তো শত্রুবল থেকে রক্ষা করতে পারলেন না আমাদের!
ঠাকুরমার প্রসাদ বিতরণের চিত্রটি জ্বলজ্বল করছে আজও। চারদিকে আমরা ঘিরে ধরতাম তাঁকে,–তিনি নির্বিকারচিত্তে প্রসাদ বিলিয়ে যেতেন। মুসলমান ভাইবোনেরাও সেদিন উদগ্রীব হয়ে থাকত প্রসাদ নেবার জন্যে। সে পুজো ছিল মানবতার পুজো-জাতিধর্মনির্বিশেষে সবাই ভক্তিসহকারে পুজোয় অংশগ্রহণ করত বলেই সেদিন সার্থক হয়ে উঠেছিল শক্তিপুজো। রাত্রে আরতির সময় বাজি ফোঁটানোর ধুম ছিল দেখবার মতো। মা ছিলেন বাজি পোড়ানোর বিপক্ষে, সামান্য শব্দও সহ্য করতে পারতেন না। তাই তাঁকে উদব্যস্ত করার দিকেই ছিল সকলের লক্ষ্য। প্রতিটি বাজির শব্দেই তিনি চমকে উঠতেন। সেদিনকার সেই শব্দ আজ আমাদেরও চমকিত করেছে–সেই বাজির শব্দই আজ প্রাণঘাতী বোমার শব্দে পরিবর্তিত হয়েছে। এখন কোথাও সামান্যতম শব্দ হলেই ভীত হয়ে পড়ি মানব-মারণ অস্ত্রের কথা ভেবে! মায়ের চমক আজ বুঝতে পারছি মনেপ্রাণে।
দশমীর দিন ভোরবেলায় বিদায়বাজনা শুনে মনটা হয়ে উঠত ভারী। বড়ো খারাপ লাগত সমস্ত দিনটা। ফুলতোলা, অঞ্জলি দেওয়া, প্রসাদ খাওয়া, ভাইবোনদের সঙ্গে হুটোপাটি করার দিন শেষ হয়ে গেল ভেবে অস্থির হয়ে উঠত মন। প্রতিমা বিসর্জন দেখে বাড়ি আসতে আর পা উঠত না। প্রণম্যদের প্রণাম সেরে নারকেল নাড়, মোয়া খেয়ে বাড়ি যখন ফিরতাম তখন বেশ রাত। শূন্য মন্ডপের সামনে আসতেই মনটা হু-হুঁ করে উঠত–যেখানে প্রাণচাঞ্চল্য ছিল কিছুক্ষণ আগেও এখন সেখানে বিরাজ করছে প্রশান্তি। উঃ! সেসব কথা মনে করতেই আজকের শোচনীয় অবস্থার কথা মনে পড়ে যায়। যেখানে প্রাণের সুখে বসবাস করেছি, আনন্দের কোলে বড় হয়েছি, আজ সেখানে মৃত্যুশীতল স্তব্ধতা। জীবনে বিজয়া দেখা দিয়েছে যেন। বছরের পর বছর পুজো আসে, কিন্তু দেশে যাবার কোনো পথ আর নেই।
মনে পড়ে বিজয়ার দিন দুর্গামায়ের কানে কানে আবার আসতে অনুরোধ জানাতাম আগামী বৎসর, কিন্তু আমাদের বিসর্জনের সময় কোনো প্রতিবেশী তো আবার ফেরার অনুরোধ জানায়নি আমাদের! এতদিনের স্নেহভালোবাসার বন্ধন এক নিমেষেই ছিঁড়ে গেল কেন? মানুষ মানুষের সঙ্গ চায় না এমন অশুভ কল্পনা তো আগে কোনোদিন করতে পারিনি আমরা। বাংলা মায়ের তরুণদল আজ দেশে দেশে শতধা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে, তাদের একত্র হবার দিন এসেছে, কিন্তু কোথায় তারুণ্য? আজ যে আমরা দেশে দেশান্তরে সতীদেহের মতো ছিন্ন হয়ে ছিটিয়ে পড়েছি, এর থেকে কোন পীঠস্থানের জন্ম হবে ভবিষ্যতে? কী লজ্জার ইতিহাসই না গড়ে তুলব আমরা! সংকটের ইতিবৃত্ত সমগ্র জাতিকে আবার মনুষ্যপদবাচ্য করে তুলুক এই শুভকামনাই করি।
আজ আর পুজোয় কোনো আন্তরিক টানই অনুভব করি না। ভোরবেলা ঘুমিয়ে আছি। কাছেই কোনো বাড়িতে রেডিয়ো খুলে দিয়েছে, ঘুমের মধ্যেই কানে বাজছে দেশের পুজোর বাজনা। চন্ডীপাঠ হচ্ছে, সুর করে স্তোত্র পড়ছেন বিরূপাক্ষ। হঠাৎ শুনি মা চিৎকার করে বলছেন—’ওরে ওঠ, আজ যে মহালয়া!’
ফুল তোলার কথা মনে পড়তেই ধড়মড়িয়ে উঠে বুঝতে পারি এ বাজনা রেডিয়োর, এ বাজনা যন্ত্রের! আমার গ্রামের পুজোর পাঠ শেষ হয়ে গেছে–হতাশায় আবার শুয়ে পড়ি। রেডিয়ো তখনও চেঁচাচ্ছে–যা দেবী সর্বভূতেষু…
সত্যি কি দেবী আবার সর্বভূতে বিরাজিতা হবেন? সকলের দুর্মতি ঘুচিয়ে দিয়ে আবার মানুষকে তিনি সুখী সচ্ছল করবেন না? সেদিনেরই প্রতীক্ষা করছি। আজ বেশি করে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী মনে পড়ছে, তিনি বলছেন, নিজের ওপর, ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস হারিয়ো না। পুণ্যের জয় হবেই, আর যা পাপ তাকে হাজার চেষ্টাতেও বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। তাই হোক, পাপের মৃত্যু হোক, নিষ্পাপ মানুষ আবার প্রাণ ফিরে পাক।
.
নাগেরগাতী
আজ আমরা সচেতনভাবে অনুভব করিব যে, বাংলার পূর্ব-পশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বহুপ্রসারিত বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন। একই ব্ৰহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিয়াছেন এই পূর্ব-পশ্চিম; হৃদপিন্ডের দক্ষিণ-বাম অংশের ন্যায় একই পুরাতন রক্তস্রোত সমস্ত বঙ্গদেশের শিরায় উপশিরায় প্রাণ বিধান করিয়া আসিয়াছে, জননী বাম-দক্ষিণ স্তনের ন্যায় চিরদিন বাঙালির সন্তানকে পালন করিয়াছে।
প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগেকার কথা। বাংলা ১৩১২ সালের ৩০ শে আশ্বিন। রাখিবন্ধনের পুণ্যমন্ত্র রচনা করে বাংলার কবি বাঙালিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন এই বলে। কিন্তু রাখিবন্ধনের ফাঁস আজ আলগা হয়ে গেছে, মানুষকে মানবতাবোধ আর সংঘবদ্ধ করতে সক্ষম হচ্ছে না। আজ মানুষের কেন এত অধঃপতন? মহাপুরুষদের বাণীর মূল্য কেন আমাদের হৃদয় জয়ে অক্ষম হচ্ছে? আমরা একপ্রাণ, একমন হয়ে এক বাংলার অধিবাসী হতে কি আর পারব না? ‘বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল–পুণ্য হউক, পুণ্য হইক, পুণ্য হইক, হে ভগবান!’–এ বাণী কি কথা হয়েই থাকবে?
বাংলার মাটি আর বাংলার জল তো আমাদের এক করে রাখতে পারল না! একই ব্রহ্মপুত্র জাহ্নবী আমাদের দৃঢ় আলিঙ্গনে বাঁধলেও আমরা তো মানুষকে সহ্য করতে পারলাম না, কোল দিতে পারলাম না ভাইকে স্বার্থসিদ্ধির কলুষ চক্রান্তে? বাপ-পিতামহের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে আসতে হল কাদের ভয়ে? কাদের হাত থেকে মানসম্ভ্রম বাঁচাবার জন্যে আমরা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে কলোনি আর ক্যাম্পে ঘুরে মরছি মা বোনদের হাত ধরে? কবে জাগবে এই যাযাবরদের ভেতর থেকে সেই মহান জ্যোতি যার আভায় আলোকিত হয়ে উঠবে দিগন্ত, কবে আবার আমরা ফিরে পাব নিজেদের দেশ-বাড়ি ঘর।
আমিও এসেছি গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া হয়ে। যারা পড়ে রয়েছে পেছনে তাদের জন্যে প্রাণ কাঁদে। কত লোক সম্ভ্রম বাঁচাতে পারেনি সামান্য গাড়িভাড়ার পয়সার অভাবে। আজ নির্জনে প্রায়ই মনে হয়, গাড়িভাড়ার পয়সা থাকলে তারাও তো আসত! বিয়োগ-ব্যথায় মন টনটন করে ওঠে সেইসব নিরুপায় মানুষের কথা ভেবে। কিন্তু গাড়িভাড়া সংগ্রহ করে আমরাই বা কী করতে পেরেছি? এ কি বাঁচা? দ্বারে দ্বারে, প্রদেশে প্রদেশে পরিব্রাজকবৃত্তি গ্রহণ করে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে–সংকটের মধ্যে পড়ে চোখের সামনে নিয়ত ভেসে উঠেছে শান্তিঘেরা পল্লিকুটিরের মায়াময় ছবিখানি। গ্রাম আমাদের ছোট্ট হোক, কিন্তু তার স্নেহ-নিবিড় সুশীতল নীড়ের তুলনা নেই। হিন্দু-মুসলমান যেখানে চিরদিন প্রতিবেশী হয়ে বসবাস করেছে তাদের মনকুসুমে কেন কীট প্রবেশ করল অকারণে?
বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে আমরাই একত্রে লড়েছিলাম, আমাদের সংঘবদ্ধ শক্তিই বণিকের রাজদন্ডকে বিপন্ন করে তুলেছে একদিন, অথচ আজ? ভ্রাতৃহত্যার নেশায় আমরা হীনবীর্য। আবার কি রাখিবন্ধন উৎসবে আমরা মেতে উঠতে পারব না কোনোদিন? রাষ্ট্রীয় জীবনে, পারিবারিক জীবনে দ্বন্দ্ব আসেই, তাকে জিইয়ে রেখেছে কোন জাতি কতদিন? আমরাই বা কেন সেই লজ্জাকর দিনের স্মৃতির জের অক্ষয় করে রাখব জীবনব্যাপী? কেন আমরা বলতে পারব না, ‘যা করেছি ভুল করেছি।’ একই জননীর স্তন্যসুধা কেন দুটি পৃথক ধারায় প্রবাহিত হবে বুঝতে পারি না।
আমরা তো কোনোদিন হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর অধিবাসী ছিলাম না,মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিনান্তের পরিশ্রমের পর সন্ধেবেলায় একত্রে জুটে সুখ-দুঃখের গল্প করেই কালাতিপাত করেছি, তবে কেন আজ পারব না সেই নিরুপদ্রব জীবন ফিরিয়ে আনতে? কেন পারব না আপনজনের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে? পারব, সেদিন বেশি দূরে নয়। আজকের অন্ধকার চিরস্থায়ী নয়, ক্ষণস্থায়ী। আবার বাংলায় সূর্যের হাসি ফুটবে–বাংলার গ্লানি দূর হবে, বাঙালি আবার যোগ্য স্থান পাবে বিশ্বের দরবারে। রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলা যায়,
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন—
এক হউক, এক হউক, এক হউক, হে ভগবান।
মনে পড়ছে আমার ছোটো গ্রামটির কথা। ময়মনসিংহ জেলার উত্তর প্রান্তে, নাগেরগাতী আমার জন্মগ্রাম, তার বুকেই কেটেছে আমার শৈশব, আমার যৌবন। সে জননী আজ আমায় বিদায় দিয়েছেন তাঁর কোল থেকে। পূর্ববাংলার সব গ্রামই প্রায় একইরকম। নদী-নালা দিয়ে ঘেরা, গাছপালায় সবুজ, ফুলেফলে সাজানো ছবির মতো। এককালে সাপের উপদ্রব ছিল বলে আমাদের গ্রামের নাম হয়েছিল নাগেরগাতী। সাপের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমরা বেঁচেছিলাম, প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলাম, কিন্তু মানুষের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ার ফলে কপালে জুটল নির্বাসন!
আমাদের পূর্বপুরুষ দু-শো বছরেরও আগে মোগলদের সময়ে এখানে এসে নাকি বসতি স্থাপন করেন। বারো জাতের গ্রাম এটা। কামার, তাঁতি, ধোপা, নাপিত, কুমোর ইত্যাদি কোনো জাতের অভাব নেই। সবার ওপরে মানুষ সত্য, তার ওপরে আর কিছু নেই– এই ছিল আমাদের আদর্শ। কুলপ্রধান ব্রাহ্মণদের লেখায়-পড়ায় স্থান ছিল অতি উচ্চে। তা হলেও গ্রামের সকলেরই সঙ্গে ছিল তাঁদের প্রাণের যোগ। গ্রামের ভেতর ছোটো বাজার–একটু দূরেই প্রধান হাট, ধান-চালের আড়ত। এখানকার সম্পদ ধান, চাল, পাট ও সর্ষে। দেশে এত শস্যসম্পদ থাকতেও আজ লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনাহারে থাকতে হচ্ছে ভেবে দুঃখই হয়।
আসামের গারোপাহাড়ের পাদদেশে আমার গ্রামখানি যেন সৌন্দর্যের মূর্তিমতী প্রতীক–আজ জনাকীর্ণ শহরে বসে সেই ছবির কথা ভেবে চোখে জল আসছে আমার। সামনে দিয়ে পাহাড়িয়া নদী কুলুকুলু শব্দে বয়ে যাচ্ছে অবিশ্রান্ত অনাবিল গতিতে। এই নদীটিই এ দেশের প্রাণ, এ দেশের সম্পদ। গারোপাহাড় থেকে হিন্দুস্থান হয়ে পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে বিজয়িনীর মতো চলেছে সে। স্থানে স্থানে কূল ভেঙে শতধা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে জলদান করতে করতে। অগভীর এই নদীর পূর্ণযৌবন আসে বর্ষাকালে। তখন তার ভয়ংকর রুদ্ররোষ চারদিকে প্লাবিত করে দেশকে করে তোলে উর্বরা,–মাঠে মাঠে চলে ফসল ফলাবার ভূমিকা। শস্যপূর্ণা বসুন্ধরার মূর্তির মোহিনীরূপ আমরা দেখি হেমন্তে। ছোটো-বড়ো নৌকা দেশ-দেশান্তর থেকে জিনিসপত্র নিয়ে আসে, নিয়ে যায়–এইভাবেই দেশের সঙ্গে বিদেশের সম্পর্ক গড়ে ওঠে ব্যাবসাবাণিজ্যের মধ্য দিয়ে। কিন্তু সে সম্পর্ক আজ শিথিল। দেশের জিনিস সব দেশেই পড়ে আছে। পাকিস্তানের ধান-পাট হিন্দুস্থানের কোনো বাজারে নেই, হিন্দুস্থানের সর্ষের তেল, কয়লা, চিনি পাকিস্তানকে চলছে এড়িয়ে! এই লুকোচুরি খেলার শেষ কোথায়? কবে আমরা ফিরে পাব অবাধ বাণিজ্যের সুখকর আবহাওয়া? সেই শুভদিন আসুক এই উপমহাদেশে!
বর্ষাশেষে অগ্রহায়ণ মাস থেকেই চলে ধানকাটার আয়োজন। কামারের বাড়ি থেকে কাস্তে শান দিয়ে সবাই চলে যায় ধান কাটতে–বিস্তীর্ণ মাঠের সোনা এনে ঘরে তোলা হয় তখন। গরিব অনাথিনীরা ধানের শিষ কুড়োতে যায়। বিদেশিরা আসে কত তৈজসপত্র নিয়ে আমাদের দেশে যা পাওয়া যায় না তার বিনিময়ে নিয়ে যায় ধান সওদা করে। ধান দিয়ে মেয়েরা কেনে কাঁচের চুড়ি, গিল্টি সোনার হার, চুল বাঁধার রঙিন ফিতে! বছরের সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসম্ভারই কেনাকাটা হয় ওই সময়।
আরম্ভ হয় চারদিকে ধান-চিড়ে কোটার আনন্দ-প্রস্রবণ। ভোর হতে-না-হতেই মেয়েরা শয্যাত্যাগ করে চেঁকিতে চিড়ে কুটছে; শব্দ হচ্ছে তালে তালে, নতুন ধানের ভুরভুর গন্ধ গ্রামকে তুলেছে মাতিয়ে। কতদিন ভেঁকির শব্দে ঘুম গেছে ভেঙে, আজও মাঝে মাঝে আচমকা জেগে উঠি আধাস্বপ্নের অস্পষ্ট শব্দ শুনে! সেসব আনন্দোচ্ছল দিন আবার জীবনে ফিরে আসবে এমন সম্ভাবনা কি নেই? আজও ভোরেই উঠতে হয়, কিন্তু সে ওঠা আর এ ওঠার মধ্যে পার্থক্য অনেক। আজ উঠতে হয় চাকরি অন্বেষণের জন্যে–দোরে দোরে উমেদারির জন্যে অমানুষিক শ্রমকে অভিশপ্ত জীবনে গ্রহণ করতে। যে সময়টা দেশে ব্যয় করতাম ফুল সঞ্চয়ের পেছনে সে সময়টা আজ যাচ্ছে ভিক্ষাবৃত্তিতে! তবুও আমরা বেঁচে আছি, আমরা তবু বেঁচে থাকব। আমরা আবার খুঁজে আনব সেই ফেলে-আসা দিনগুলোকে। প্রতিবেশীর মুখে হাসি না দেখে মরব কোন আনন্দ নিয়ে?
আমাদের গ্রামবাসীদের চেহারায় কোনোদিন মালিন্য দেখিনি। সুন্দর অটুট স্বাস্থ্য নিয়ে চাষিরা প্রত্যূষে চলে যেত মাঠে। আর মেয়েরা প্রস্তুত করত খাবার–গৃহস্থালি কাজের মধ্যে ঝরে পড়ত তাদের গৃহিণীপনার লালিত্য। জীবনে কি আবার ফিরে আসবে না সেসব দিন আবার কি সেসব মানুষ গান গাইতে গাইতে কাঁধে লাঙল নিয়ে যাবে না মাঠে? গৃহিণীরা তৈরি করবে না পিঠে-পুলি, করবে না গৃহস্থালির খুঁটিনাটি কাজ? জানি না আজ কেন এত করে মনে পড়ছে ছেড়ে-আসা গ্রামকে, নগরজীবনে গ্রামের কথা এত মাথা তুলে কেন দাঁড়াচ্ছে বারবার মনের আয়নায়?
যেসব রীতিনীতিকে কেন্দ্র করে সমাজজীবন গড়ে উঠেছিল তা ভেঙে গেছে। সবার সঙ্গেই ছিল আমাদের আত্মীয়তা। কেউ কাউকে নাম ধরে ডাকত না-দাদা, মামা, চাচা যোগ না করলে সামাজিক জীবনে হত ক্ষমাহীন অপরাধ। আজ কোথায় সেসব সম্পর্ক তলিয়ে গেল ঘূর্ণির মধ্যে, কে কোথায় বিক্ষিপ্ত হয়ে স্নেহের শ্রদ্ধার সম্বন্ধ হারিয়ে তাচ্ছিল্যের মালা গলায় পরে জীবন বাঁচাচ্ছে কে জানে। শিশুরা মরছে দুধের অভাবে, মায়ের বুক থেকে আজ আর সুধাঁধারা ক্ষরিত হচ্ছে না–দেশজননী এবং মা জননী রক্ষা করতে পারছেন না তাঁদের সন্তানদের। এর চেয়ে দুর্দিন আর কী হতে পারে? কোন দেশের ইতিহাসে রয়েছে এমনি অমানুষিক বর্বরতার দৃষ্টান্ত? কবে মহামিলনের মন্ত্র কার্যকরী হবে তা না জানলেও এমন দুর্দিন মানুষের জীবনে বেশিদিন স্থায়ী হবে না তা জানি।
শারদীয় পুজোয় গ্রামের আনন্দ হত বল্গাহীন, ইতর-ভদ্র সবাই মেতে উঠত আনন্দময়ীর আগমনে। কী অপূর্ব মহামিলনের উৎসব! মনের সকল সংকীর্ণতা মুক্ত হয়ে সবাই যেন উদার মহান হয়ে উঠত। দেখেছি সে স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধার আসল চেহারা, দেখেছি সেদিনকার লোকখাওয়ানোর অনাবিল আনন্দ। পুজো, আরতির ধুম, ছেলে-মেয়েদের নাচ, ঢাক-ঢোল বাঁশির বাজনায় ফেটে পড়ত সন্তান গৌরবিনি আমার গ্রাম-জননী। পুজোর চারদিন উৎসব ছেড়ে কেউ কোথাও নড়ত না, ভাব-বিভোরতায় মাতোয়ারা হয়ে থাকত সবাই। বিজয়ার দৃশ্য আজও ভাসছে চোখে। আমাদের নদীর ঘাটেই নানা গ্রামের নানা প্রতিমার নৌকা গান-বাজনা করতে করতে এক জায়গায় এসে জড়ো হত। মাঝে মাঝে ধ্বনি উঠত : বন্দেমাতরম! ভারতমাতার সেইদিনকার বন্দনার প্রতিদানেই কি আমাদের আজকের এই সর্বহারা রূপ? এ কি মায়ের আশীর্বাদ, না জ্বলন্ত অভিশাপ? এ যে অভাবনীয়। সন্তান অন্যায় করলেও মা কী পারেন এমনি কঠোর হতে? হয়তো শক্তিপুজোয় ফাঁকি ছিল আমাদের, যতখানি ভক্তি অর্ঘ্যের প্রয়োজন ছিল তা আমরা দিইনি, তাই জাতীয় যুপকাষ্ঠে বলি হয়ে গেল দেশ।
ত্যাগের মধ্য দিয়েই ভোগের আস্বাদ নিবিড় করে পাওয়া যায়। আমরা আধ্যাত্মিক ভারতের অমৃতের পুত্র। তাই সুখ ত্যাগ করে আজ আমরা তামস তপস্যায় রত। এ তপস্যায় রত হয়েছে হিন্দু, এ তপস্যায় রত হয়েছে মুসলমান। শবসাধনায় শোধিত হয়ে দেশমাতৃকা জ্যোতির্ময়ীরূপে আবির্ভূত হন এ প্রার্থনা কার নয়? ভুক্তভোগী মানুষ মানুষের সপক্ষে; তারা শান্তি চায়, শুধু শান্তি চায়, আবার সুখী-সচ্ছল হয়ে বাঁচার মতো বাঁচতে চায়। সব মানুষের এক প্রার্থনা হলে মা বেশিদিন কিছুতেই থাকতে পারবেন না সন্তানদের পৃথক করে রেখে।
মনে পড়ছে বেশি করে চৈত্র সংক্রান্তির কথা। এই দিনটির কথা কোনোদিন ভোলা সম্ভব নয় নাগেরগাতীর ছেলে-বুড়োদের। ধনী-দরিদ্র, চাষি-জমিদার সবাই তাদের গৃহপালিত গোরু-ঘোড়াকে নদীর জলে স্নান করিয়ে এনে নানা রঙে বিচিত্রিত করে দিত তাদের সর্বশরীর। ধূপ-ধোঁয়া দিয়ে কামনা করা হত তাদের মঙ্গল। চাষিরা দিনে অনাহারে থেকে নতুন কাপড় পরে নতুন আনন্দে বর্ষশেষের এই দিনটিকে জানাত প্রাণের ভক্তি-শ্রদ্ধা। তাদের একমাত্র সম্বল বাঁচবার আশা-ভরসা, তাদের বলদ-গাভীর দীর্ঘজীবন কামনায় ছোটো ছোটো চাষি-বালক-বালিকারাও আনন্দে দিশাহারা হয়ে পথে পথে বেড়াত নৃত্য করে। কিছুদিন আগেও খবর পেয়েছি আর সেদিন নেই,–নিঃশব্দে বছর চলে যায়। লোকজনের অভাবে এখন আর কোনো আড়ম্বরেরই সাড়া নেই অত বড়ো গ্রামে।
চৈত্র সংক্রান্তির বিকেলবেলায় আমাদের গ্রামে হত ষাঁড়ের লড়াই। কী উৎসাহ কী উদ্দীপনা নিয়েই না এই লড়াই দেখেছি একদিন। দূর দূর গ্রাম থেকে হিন্দু-মুসলমান চাষিরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে তাদের ষাঁড়কে নানা রঙে সাজিয়ে, ফুলের মালা দিয়ে, শিং-এ রঙিন রুমাল বেঁধে জারিগান গাইতে গাইতে এসে জড়ো হত নির্দিষ্ট মাঠে। তারপর চলত সেই বহুপ্রতীক্ষিত লড়াই। যে দলের ষাঁড় জয়লাভ করত তারা যুদ্ধজয়ের পুরস্কার হিসেবে পেত জমিদারবাবুদের দেওয়া কত জিনিস। এইদিনের লোক সমাগম হত দেখার মতো–মোড়ল মাতব্বরেরা শান্তিরক্ষা করতে হিমসিম খেয়ে যেত সেদিন। লাঠির জোরে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হত। সেদিনকার সে দৃশ্য মনে পড়লে আজও গুমরে ওঠে মন। আমরা অনেক আগে থেকেই গাছে আশ্রয় নিয়ে নিরাপদ দূরত্ব থেকে লড়াই-এর রোমাঞ্চ অনুভব করতাম। এক বিচিত্র আশা-আকাঙ্ক্ষায়, উত্তেজনা-ঔৎসুক্যে ভরপুর হয়ে উঠত মন।
সেদিন গাছের দৃশ্যও যেত পালটে,–গাছে গাছে মানুষ ঝুলছে বাদুড়ের মতো! মাঝে মাঝে দুর্ঘটনাও যে ঘটত না তা নয়,–ভালো করে দেখবার জন্যে এক এক সময় হুটোপুটিও লেগে যেত জায়গা দখল নিয়ে! ডাল ভেঙে সেবার যে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছিল তার কথা ভোলা যায় না। অবশ্য রক্তাক্ত প্রতিবেশীর অসাড় দেহ দেখে সেদিন যতটা উতলা হয়েছি, আজ আর তেমন হয় না। মানুষের মৃত্যুতে স্বাভাবিক বেদনাবোধের সে অনুভূতি গেল কোথায়? বিকৃত দেহ সম্বন্ধে সেদিন ধারণা স্পষ্ট ছিল না, আজ স্বচ্ছ হয়েছে। চোখের সামনে কত প্রিয়জনের মৃত্যু যে দেখেছি তা বর্ণনা করে লাভ নেই। ষাঁড়ের লড়াইকে আজ প্রতীক বলেই মনে হচ্ছে আমার, নিরাপদ দূরত্বে বসে নিশ্চয়ই কোনো দর্শক উপভোগ করছে এ দৃশ্য! তারও কি পতন ও মৃত্যু হবে না সমস্ত লাঞ্ছিত অপমানিত মানুষের অভিশাপে?
আজ আমরা যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছি তাতে পূর্ববঙ্গ গীতিকার আয়না বিবির খেদের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়,
যেই রে বিরক্কের তলে যাই আরে ছায়া পাওনের আশেরে।
পত্র ছেদ্যা রৌদ্র লাগে দেখ কপালের দোষে রে।।
দইরাতে ডুবিতে গেলে দেখ দইরা শুকায় রে।
গায়ের না বাতাস লাগলে আর ভালা আগুনি ঝিমায় রে।।
কতকাল আগেকার কোন সে অজ্ঞাত প্রাচীন কবি বাঙালি নর-নারীর চিরন্তন প্রেমকাহিনি রচনা করতে বসে দিব্যদৃষ্টিতে পূর্ববাংলার একালের অধিবাসীদের চরম অসহায়তা উপলব্ধি করেই হয়তো এমনি ছত্রে ছত্রে ফুটিয়ে তুলেছিলেন ছেড়ে-আসা গ্রামের ভবিষ্যৎ বাঙালির মর্মবেদনা। স্বাধীন দেশের বৃক্ষতলায় শান্তির নীড় বাঁধব, শঙ্কাহীন মনে নবজীবনের বন্দনা গান গাইব, সে সুযোগ আমাদের কবে হবে?
.
সাখুয়া
মেঘে মেঘে আকাশ গেছে ছেয়ে, চারদিকে নিবিড় সন্ধ্যার অকালবোধন। ঘন অন্ধকার যেন গলা চেপে ধরেছে! এ মেঘ রাজনৈতিক মেঘ, এর বৃষ্টি আনে অশ্রুজলের বন্যা! একদিন যা ছিল আমার জন্মভূমি আজ নাম হয়েছে তার ‘ছেড়ে-আসা গ্রাম’। আকাশে কালো মেঘের সারি, পুব থেকে পাড়ি জমিয়েছে পশ্চিমের দিকে। হু-হুঁ করে ছুটে চলেছে দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে দেশ-দেশান্তরে, দূর-দূরান্তরে অসহায় নিঃসহায়ের মতো। এত মেঘ পুবদিকে ছিল কোথায়? কোথা থেকে জন্ম নিল সর্বনাশা এই কালো মেঘ? মেঘের ডমরুর গুরু গুরু শব্দে আমরা ভীত হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারিনি যে, তার বর্ষণ এত নির্মম হতে পারে, শোনা ছিল ‘যত গর্জে তত বর্ষে না। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে সে মেঘ যত গর্জিয়েছে তার চেয়েও বর্ষিয়েছে বেশি! আজ লজ্জায় মরে যাই সেদিনের সেই আত্মগ্লানির কথা ভেবে! কোথায় গেল আমার সেই জন্মভূমি, সোনার প্রতিমা ‘সাখুয়া গ্রাম? আমার সাখুয়া মা আমাকে চিরদিনের মতো ত্যাগ করেছে। আমার গাঁয়ের মাটি আমাকে ধরে রাখতে পারল না–অথচ তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তো আমাকে বারবার বলেছে ‘যেতে নাহি দিব। উঠোনের মাধবীতলার ফুলগুলো, বাগানের মল্লিকা, জুই, বেলফুল আমাকে গন্ধে মতোয়ারা করে দিয়েছিল চলে আসার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্তও। যেদিকে তাকিয়েছি সেই দিকেই অনুভব করেছিলাম স্নেহের পরশ; তবু আসতে হল, ভিক্ষাপাত্র সম্বল করে মহানগরীর অবাঞ্ছিত নাগরিক সাজতে হল শত অনিচ্ছাতেও। কেন এমন হল, কেন আমার ওপর কূপিত হলেন আমার পল্লিমা?। কারণ পাই না,কারণ খুঁজতে ইচ্ছেও করে না। শুধু ইচ্ছে করে মায়ের রূপ ধ্যান করতে, চোখের সামনে আমার জীবন্ত গ্রামটিকে ধরে রাখতে। আশা আছে মায়ের কোলে আবার স্থান পাব–উত্তেজনার ঘোরে মায়ের করুণা হারিয়েছি ক্ষণিকের তরে, এটা দীর্ঘস্থায়ী নয়। হয়তো তিনি বলেছিলেন–’চল তোরে দিয়ে আসি সাগরের জলে’ অসতর্ক ক্ষণে, কিন্তু মায়ের এই কথা শুনে ভুল করলে চলে না,-এমন অলক্ষুণে কথা কোনোদিন মা বলতে পারেন না মনেপ্রাণে। কথাতেই তো আছে, কুপুত্র যদিও হয় কুমাতা কখনো নয়। আমার সাখুয়া মা আবার আমাকে কোলে স্থান দেবেন, আমি আবার গাইতে পারব—’এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।’
পেছন থেকে মগরা নদী যেন আমার গ্রামটিকে সহসা ধরেছে সোহাগ করে চেপে। দুরন্ত ছোট্ট নদী যেন সাখুয়ার আঁচলের তলায় নির্ভয়ে থাকতে চায় দুরন্ত মেয়েটির মতো। তরতর করে তাই তার অমন নেমে চলা গতি! মগরা নদী আমাদের জীবনে এনেছিল স্নিগ্ধতা, গ্রামটিকে করেছিল উন্নত নানা দিক থেকে। মগরার স্রোতে আমাদের জীবনস্রোত একাত্ম হয়ে মিশে পেয়েছিল পরিপূর্ণতার স্বাদ।
আজ কত স্মৃতি এসে ভিড় করছে মনের কোণে–নির্জনতা পেলেই তারা আমাকে উতলা করে বারবার। ভুলতে পারি না, তার কথা না ভেবে শান্তি পাই না। যাকে প্রাণভরে ভালোবাসি তার স্মৃতিই লাগে মিষ্টি। ক্ষীণ স্মৃতি যে পুরোনো কত তথ্যকে উদঘাটিত করে তা ভুক্তভোগীরাই জানেন। মনে পড়ছে, শান্তিতে ঘেরা সাখুয়ার ভিন্ন ভিন্ন পাড়ার কথা। হিন্দু আর মুসলমান পাড়া। সামনেই বিরাট ফসলের জমি। মাঠের পশ্চিম সীমানায় হিন্দু মুসলমানের পাশাপাশি বসতি-সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাগত সেখানে প্রাণকণিকা, জ্বলজ্বল করত শিশিরভেজা ধানের শিষগুলো! ভোরবেলা দূর্বাদলের মাথায় টলমল করত মুক্তোর মতো স্বচ্ছ শিশিরকণা। মানসচক্ষে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি সেদিনের উধাও হওয়া মনের চেহারাখানি। ভোরে উঠেই বেরিয়ে পড়তাম ভিজে ঘাসের স্নিগ্ধ পরশ নেবার লোভে। চারদিক নিঝুম, আমি বেপরোয়াভাবে শুধু যেতাম এগিয়ে দূরের গ্রামের দিকে চলার নেশায়। সূর্য উঠেছে আর আমি উঠিনি এমন কোনোদিন হয়নি। একদিন মনে পড়ে, মহাবিপদের মধ্যে পড়েছিলাম আলে আলে চলতে গিয়ে। আমি তখন ছোটো, অভ্যাসমতো ভোরে বেড়াতে বেরিয়েছি ঠাকুরদার সঙ্গে। ঠাকুরদা বুড়োমানুষ, পারবেন কেন আমার চাপল্যের সঙ্গে পাল্লা দিতে! ছুটে ছুটে এগিয়ে গেছি অনেক দূর-হঠাৎ একটা দৃশ্যে আমি হয়ে গেলাম হতভম্ভ। আলের ওপর আড়াআড়ি হয়ে শুয়ে আছে মস্ত এক সাপ। ভয়ে আমি গতিহীন,–নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমরা পূর্ববঙ্গের লোক, সাপ আমাদের ভয় দেখাতে পারে না। আমি ছোটো বলেই হয়তো ভয় পেয়েছিলাম সেদিন। ঠাকুরদা আমার নির্দেশিত সাপটি দেখে একগাল হেসে শুধু বলেছিলেন–’বোকা কোথাকার, এখনও সাপ চিনিস না? ওটা সাপ নয় রে, সাপের খোলস, বুঝলি,–আসল সাপ বিশ্রাম করছে গর্তের ভেতর!’
সেদিনের ছোটো ছেলেটি আসল-নকলের পার্থক্য ধরতে পারেনি সাপের, আজকেও আমি কি ধরতে পেরেছি মানুষের আসল-নকল রূপ? বারবার প্রশ্ন করেছি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছি কিন্তু পদে পদে ব্যর্থ হয়েছি সমাধান খুঁজতে গিয়ে। তাই আজ সবচেয়ে বেশি করে মনে পড়ছে ঠাকুরদার কথা,–তিনি থাকলে ভাবতে হত না এত খুঁটিয়ে! মানুষ চেনা দেখছি সব চেয়ে কঠিন ব্যাপার! যে মানুষকে বিশ্বাস করেছি, যে মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তা করেছি, সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হয়েছি, আজ কোথায় তারা? ছোটোবেলায় রূপকথা শুনে কতদিন আঁধার রাতে মাঠের দিকে তাকিয়ে দেখতে চেয়েছি তেপান্তরের মাঠে রূপকথার রাজপুত্তুরকে পক্ষীরাজ ঘোড়ার সোয়ারি বেশে, তারায় ভরা আকাশের নীচে ঝিল্লিমুখর প্রান্তরের বুকে কৈশোরের স্বপ্ন ভেঙে খানখান হয়ে গেছে বারবার, আজকের স্বপ্নেরই মতো।
আঁকাবাঁকা খেতের আলে ছোটো ছোটো পা ফেলে পাঠশালায় যাবার কথা মনে পড়ছে। শিক্ষক ছিলেন দুজন, দুজনই মুসলমান। আজও তাঁরা আছেন কি না জানি না। তাঁদের একজনের কথা আজ বিশেষ করে মনে পড়ে। আমার বি. এ. পাশের সংবাদ পেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন আমার শৈশবের সেই মাস সায়েব–আন্তরিকতায় পূর্ণ সে চিঠি। আমার কাছে তা অমূল্য সম্পদ, তাই সযত্নে রেখে দিয়েছি বাক্সে। বহুমূল্যবান জিনিস ছেড়ে এলেও সে চিঠি হাতছাড়া করিনি। ন্যূজ দেহ, ক্ষীণ দৃষ্টি, বার্ধক্যের ভারে ক্লান্ত, শুভ্র লম্বা দাড়ি নেড়ে তিনি আমাদের পড়াতেন। কত অমূল্য উপদেশ দিতেন গল্পচ্ছলে,-একদিনের পরিচয়েই জানতে পেরেছিলাম তিনি মানবধর্মের পূজারি। মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাতে তিনি বারবার বারণ করেছিলেন আমাকে। বলেছিলেন–”সমস্ত মানুষের শুভবুদ্ধি একদিন জাগবেই। শিহরন লেগেছিল শেষকথাটির ওপর জোর দেওয়াতে। মাস সায়েবে’র কথায় বিশ্বাস আমি হারাইনি, তাঁর কথাই সত্যি হোক এ প্রার্থনা করি। আশায় বুক বেঁধে রয়েছি সেই সুদিনের নবপ্রভাতের জন্যে। জানি না সে সূর্যোদয়ের বিলম্ব কত!
ছোটোবেলাকার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল রউফ। একসঙ্গে পড়তাম, স্কুলে যেতাম, খেলাধুলো, স্নান, সাঁতার ছিল সবই একসঙ্গে। আমাদের দুটিকে একত্রে সর্বদা সব জায়গায় দেখা যেত বলে অনেকে উপহাস করে বলতেন ‘মানিকজোড়’–আর যাঁরা আরও তীব্র রসিকতাপ্রিয় ছিলেন তাঁরা বলতেন রাম-রহিম’। আমরা কান দিতাম না সে-কথায়, বন্ধুত্বে চিড় খাওয়াতে রাজি ছিলাম না। আমাদের বাড়িও ছিল পাশাপাশি, বাড়ির মাঝখানে শুধু একটা ধানখেতের ব্যবধান। তখন তাই মনে হত যেন কত দীর্ঘ। কিন্তু আজকের এই দীর্ঘ ব্যবধান তো কারও মনে তেমন করে দোলা দিতে পারছে না। আমি রউফের কথা ভাবছি। রউফও কি ভাবছে আমার কথা পাকিস্তান থেকে আমারই সুরে সুর মিলিয়ে?
একদিনের এক হাস্যকর ব্যাপার মনে পড়ে! রউফ একদিন আবিষ্কার করে ফেলল হঠাৎ যে, আমাদের সঙ্গে ওদের বাড়ির একটা প্রভেদ আছে মুরগি পোষা নিয়ে। এইজন্যেই হয়তো আমাদের দু-বাড়ির ব্যবধানও একটু বেশি! বাড়ি গিয়েই সে সেই রাত্রেই সব কটি মুরগি চুপি চুপি চালান করে দিয়ে এল আর এক বাড়িতে। সে মুরগি অবশ্য ফিরে এসেছিল রউফদের বাড়িতেই আর তার কীর্তির কথাও রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বন্ধুর সঙ্গে সমস্ত প্রভেদ ঘুচিয়ে নিকটতম হওয়ার এই যে ছেলেমানুষি বুদ্ধি এবং আন্তরিকতা তার তুলনা কোথায়? এই যে কাছের মানুষ করে নেবার প্রচেষ্টা, আজ সেই সরল মনের নির্বাসন হল কেন এতদিন একত্রে থাকার পরেও? মনের গড়ন কেন মানুষের বদলাল রাতারাতি! আজকেও সেইদিনকার মতোই ভাবি সময় সময়, রউফ আর আমার মধ্যে ব্যবধান কোথায়? আমরা দুজনে অভিন্নহৃদয় বন্ধু, আমরা মানুষ। তখন কি ভুলেও ভাবতে পেরেছি যে, রউফের সঙ্গে চিরকালের মতো হবে ছাড়াছাড়ি? যে সাখুয়াকে চোখের আড়াল করা দুঃসাধ্য ছিল তাকেও এমনি ছাড়তে হবে, ভেবেছি কি কোনোদিন? কোথায় গেল আমার প্রাণের বন্ধু, কেথায় গেল আমার গ্রাম! আকুল হয়ে ভাবি আর মাথা ঠুকি ভাঙা শান-বাঁধানো মেঝেতে না, এখানে মাটির স্পর্শ নেই। চোখ-ধাঁধানো নির্মম কলকাতা পল্লিমায়ের মধুমিষ্টি শান্তির প্রলেপ দিতে পারে না। যান্ত্রিক শহর, অত্যাশ্চর্য তার আকর্ষণী শক্তি মানুষকে অমানুষ করার দিকে। মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু দেখছি এখানে প্রত্যহ! তবু একে কত আদর, কত সোহাগ! এই প্রাসাদপুরীর ঐশ্বর্যের হিংস্র ঔদ্ধত্যের কাছে মানবতার দোহাই হাস্যকর!
সাখুয়ার মাঠ হিন্দু-মুসলমানের বারোয়ারি সম্পত্তি। খেত চষা, বীজ বোনা থেকে আরম্ভ করে ফসলকাটার দিন পর্যন্ত বিশাল সেই মাঠের বুকে সম্মিলিত শ্রম চলত পাশাপাশি পরস্পরের সুখ-স্বপ্নের অংশীদার হয়ে। সবচেয়ে ভালো লাগত জারি গানের সুরে সুরে। খেতের বুকে অলৌকিক আনন্দের ঢেউ জাগাতে। গলা ছেড়ে তামাক খেতে খেতে গান ধরত তারা সমবেত গলায়,
ওরে অমর কেউ থাকবি না তো, মরতে হবে সবারে,
তবে সংসারে তোর এত ভেদ-জ্ঞান কীসেরি তরে।
এ গান যারা গাইতে পারে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্নেহ-প্রীতি, ভালোবাসা কত অকৃত্রিম ছিল সহজেই বোঝা যায়। এই পরিবেশে কোথা থেকে এল সর্বনাশা এই ভেদজ্ঞান?
সাখুয়ার ‘বড়োঘাট’ও সর্বজনীন। এখানেও গাঁয়ের সকলেরই সমান অধিকার। মনের খুশিতে সবাই স্নান করছে, সাঁতার কাটছে, জল নিচ্ছে বিনা দ্বিধায়। গরমের দিনে ঘাটের কোলে জেলাবোর্ডের রাস্তার পাশে সবুজ ঘাসের ওপর বসত মজলিশ-নিশুতি রাত্রি অবধি চলত আলোচনা। তর্ক হত, কিন্তু সহিষ্ণুতার কোনো অভাববোধ ঘটেনি কোনোদিন। আলোচনায় যোগদান করত তরুণ সমাজ। সেখানে চলত দুঃখের কথা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা, গ্রাম্য রাজনীতি থেকে শিক্ষাদীক্ষা এমনকী আজকের সংস্কৃতির গতি-প্রগতির কথাও বাদ যেত না। আলোচ্য বিষয় আলোচনার আবহাওয়ার ওপর ওঠানামা করত। বয়স্কদের সব বৈঠক হত মথুর মাস্টারের বৈঠকখানায়। ক্রমাগত তামাক পুড়ত সেখানে, তিনটে হুঁকো হিমসিম খেয়ে যেত বক্তাদের শোষণের ঠেলায়! কল্কে পুড়ে লাল হয়ে উঠত, ফাটবার উপক্রম! মথুর ঠাকুর ছিলেন ভিনগাঁয়ের স্কুল মাস্টার, জ্ঞান ছিল গভীর, মানুষ হিসেবে ছিলেন একেবারে ভোলানাথ। লোকের দুঃখে তিনি বিচলিত হতেন বলেই সকলেই ছুটে আসত পরামর্শ নিত। পরামর্শ বা সাহায্য দিতে কোনোদিন দ্বিধা করতে দেখিনি তাঁকে। গোলমালে পড়লে পাড়ার মাতব্বরেরাও লজ্জা করতেন না তাঁর কাছে আসতে। শুনেছি আজও তিনি দেশ ত্যাগ করেননি,–আঁকড়ে পড়ে আছেন দেশের বাড়িতে। তিনিও আশা করেন একদিন না একদিন জাতীয় কলঙ্কের অবসান হবেই, আবার উন্মত্ত মানুষ দুর্যোগের রাত্রি কাটিয়ে প্রকৃতিস্থ হবে নতুন জীবন-প্রভাতে। ঘুচে যাবে আজকের সংকট, মুছে যাবে লজ্জার ইতিহাস।
প্রতিরবিবার হাট বসত মগরা নদীর তীরে। একদিকে জেলাবোর্ডের বড়ো রাস্তা, অন্যদিকে মগরা নদী। একদিকে গোরুর গাড়ির ভিড়, অন্যদিকে সারি সারি পালতোলা নৌকা। কোলাহলমুখর হাট এনে দিত সপ্তাহান্তে কল্লোলিত প্রাণের আনন্দোচ্ছাসের ঢেউ। প্রতীক্ষা করে থাকতাম রবিবারের জন্যে-লক্ষ করেছি সেদিনকার মানুষে মানুষে সম্প্রীতির সম্বন্ধ। ইসমাইল চাচার চালের গোলার পাশেই ছিল রজনীমামার কাপড়ের দোকান। আমরা হাটে গেলে উত্যক্ত করে ব্যস্ত করে তুলতাম ইসমাইল চাচাকে! খরিদ্দারের সঙ্গে কথা বললে আমরা জোর করে তাঁর মুখ ঘুরিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বাধ্য করতাম। আমাদের শয়তানি থেকে মুক্তি পাবার জন্যেই হয়তো চাচা বড়ো বড়ো মাছ-লজেঞ্চুস রাখতেন লুকিয়ে,–একটা একটা পেলে তবেই নিষ্কৃতি দিতাম তাঁকে! সেদিনকার এই দুষ্টুমির কথা ভেবে একটু একটু লজ্জা হলেও আনন্দটাই হয় বেশি। আজ রজনীমামা কলকাতার পথে পথে ফিরি করে বেড়ান, অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটে তাঁর।
পুজো-পার্বণ, ইদ-মহরমেই পেতাম মানুষের মনের আসল পরিচয়। বিজয়া দশমী এবং ইদ আমাদের গ্রামে ছিল মিলনের প্রতীক। বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রীতি-বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে করতে হত মিষ্টিমুখ। সেই আনন্দমুখর দিন কি আর ফিরে পাব না আমরা। সেদিনকার মানুষরা আজ কোথায়?
আজ মনের পর্দায় ভেসে ওঠে মহুয়ার গান, গুনাইবিবির পালা, বাউল গান, জারি গান, কবির লড়াই, মনসার ভাসন, গাজির গানের আসরের জনবহুল দৃশ্যের টুকরো টুকরো ছবি। জাতিধর্মনির্বিশেষে নির্বাক শ্রোতার দল গ্রহণ করেছে এসব সংগীতরস। ব্রাহ্মণের ছেলে নদের চাঁদ, আর মুসলমানের মেয়ে মহুয়া; মুসলমান গায়ক ও সাধক গাজি আর হিন্দুর মেয়ে চম্পাবতী–অবাক হয়ে দেখেছি নদের চাঁদ আর মহুয়ার দুঃখে, গাজি আর চম্পার ব্যথায় সমভাবে অশ্রু বিসর্জন করছে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নর-নারীই। সকলেই নাটকবর্ণিত দুঃখকে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের দুঃখ বলে গ্রহণ করেনি, করেছে সমস্ত মানুষের দুঃখ হিসেবেই। তাই তো সহজেই তারা হতে পারত সবাকার সুখ-দুঃখের অংশীদার।
পৌষ সংক্রান্তিতে আমাদের হাটে বসত মেলা। ঘরে ঘরে তখন চলত নবান্নের উৎসব, সকলের মুখে হাসির ছোঁয়াচ। গ্রামের ওস্তাদ মেঘু শেখ ছিলেন বিখ্যাত কুস্তিগির, তাঁর সুযোগ্য শিষ্য ছিলেন আমার জ্যাঠামশায়। জ্যাঠার অকালমৃত্যুতে দেখেছি অমন জোয়ান মেঘু শেখও হয়েছিলেন পাগলের মতো। পুত্রশোক পেয়েছিলেন যেন জ্যাঠামশায়ের মৃত্যুতে। সেইদিন থেকে আর কেউ তাঁকে কুস্তি লড়তে দেখেনি। সব কিছু ছেড়ে দিয়ে নিঃসন্তান ওস্তাদ আজও বেঁচে আছেন। আমাদের সঙ্গে দেখা হলে অবিশ্রান্তভাবে তিনি শুধু জ্যাঠামশায়ের গল্পই বলে যেতেন, আর অশ্রুধারায় তাঁর গন্ডদেশ যেত ভিজে। তেমন স্নেহ আজ পর্যন্ত দেখিনি। আজ সেই স্নেহপ্রবণ মন কোথায় গেল মানুষের!
এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথা না বললে আমার স্মৃতিকথা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সে আমাদের গ্রামের চারণ কবি-কবীর পাগল। জাতিতে সে মুসলমান হলেও কোনো ধর্মের ওপরই বিরাগ ছিল না তার। সমস্ত ধর্মকেই বিশ্বাস করত কবীর পাগল। সেও আজ বৃদ্ধ। কিছুদিন আগে শুনেছি সে নাকি অন্ধ হয়ে গেছে। গ্রামের এবং জাতির জন্যে একটি ইতিহাসের মালা গেঁথে রেখেছে কবীর গানের সুরের সূত্র দিয়ে। ছোটোবেলা থেকেই দেখেছি ধর্মের সমন্বয়ের দিকেই তার ঝোঁক। ভিক্ষের অজুহাতে বাড়ি বাড়ি গান গেয়ে বেড়াত সে। রামায়ণ-মহাভারত-কোরান-বাইবেলের গল্প শুনেছি তারই মুখে প্রথম। তাকে কেউ বলত বৈষ্ণব, কেউ বা ভাবত ফকির। আমার সঙ্গে রউফের একবার ঝগড়া হয়ে কথা বন্ধ হয়ে যায়। মনে পড়ে কবীরই করে দিয়েছিল তার মীমাংসা। তার সামনে মনে পড়ে প্রতিজ্ঞাও করেছিলাম-বন্ধুতে বন্ধুতে, ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া হতে দেব না কোনোদিন। আমাদের ঝগড়া মেটাতে গিয়ে সে কেঁদেছিল সেদিন। ছোট্ট ছেলে বলেই সে কান্নার অর্থ বুঝিনি তখন। আজ এক-একদিন রাত্রে কার ডাকে ঘুম ভাঙতেই মনে পড়ে যায় যেন; সকলের আগে মনে পড়ে কবীরের মুখখানি। কবীর নিশ্চয় আমাদের দুঃখ নিয়েও গান রচনা করেছে। আজ সে অন্ধ, কিন্তু মানসচক্ষে তো মানুষের বেদনা দেখতে পাচ্ছে সে। আজ চমকে চমকে উঠি গানের রেশ শুনলে, বাউল-ভাটিয়ালি হলেই কবীর মনের সামনে এসে দাঁড়ায়। মনে পড়ে যায় তার ‘ফিরে আয়, ওরে ফিরে আয়’ গানখানি। মনে পড়ে যায় সে-ই বলেছিল মাস্টার সায়েবের মতো দৃঢ়কণ্ঠে–’ভাইয়ে ভাইয়ে, বন্ধুতে বন্ধুতে আবার মিলন ঘটবেই, পৃথিবী হবে সুন্দর। আমরা তোমার কথা বিশ্বাস করি কবীর, আমাদের দেশ আবার সকলের হবে, সমস্ত শয়তানের মৃত্যু হবে একদিন। তবে সেদিন তোমায় পাব কি না জানি না!
যশোহর – অমৃতবাজার সিঙ্গিয়া
নিজের গ্রাম সম্পর্কে কিছু বলতে হলে প্রথমেই কী মনে আসে আপনার? মাটি আর মানুষ দুই-ই। দেশের মাটিতে ফলে ফসল, আর সে-ফসলের অংশীদার মানুষ গড়ে তোলে গ্রামের সম্মান ও সমৃদ্ধি। আজ নিজের গ্রামকে বিশেষভাবে লক্ষজনের সানুরাগ দৃষ্টির সম্মুখে তুলে ধরবার এই প্রচেষ্টা উত্তর-কাল কীভাবে গ্রহণ করবে কে জানে? ছেড়ে এসেছি যে গ্রাম, এ কি তার জন্যে অশ্রুবিসর্জন? না কি ছায়াসুনিবিড় সেই জন্মভূমির প্রিয় সযত্নলালিত স্মৃতি নিয়ে এ এক ঐতিহ্যবিলাস? এ প্রশ্নের জবাব আজ নাই-বা দেওয়া হল। তবু গ্রামের কথা বলতে বসে প্রথমেই মনে পড়ছে, দেশব্দলের পালায় শরণার্থীর অশ্রু দিয়ে জন্মভূমির এ অর্ঘ্য হয়তো একেবারে ব্যর্থ হবে না। হয়তো গ্রামের মানুষ আবার তার গ্রামকে গভীরতর মমতায় ফিরে পাবে শান্তি ও মৈত্রীর মধ্য দিয়ে।
কলকাতা-খুলনা রেললাইনে যশোহর জেলার ঝিকরগাছা স্টেশন কোনোদিন দেখেছেন? ঝিকরগাছা এ অঞ্চলের অন্যতম বৃহৎ স্টেশন। সুদীর্ঘ সুরকির প্ল্যাটফর্ম, সন্ধ্যার নরম অন্ধকারে ট্রেনটি গিয়ে পৌঁছেলেই গ্রামের গন্ধ পাওয়া যায়। পাশেই স্বচ্ছসলিল কপোতাক্ষ নদ। ঝিকরগাছা থেকে চার মাইল দূরে এনদের এপারে আমার গ্রাম অমৃতবাজার। অমৃতবাজারের পূর্বনাম পলুয়া-মাগুরা। গত শতাব্দীর মধ্যভাগে নদিয়া জেলার হাঁসখালি গ্রাম থেকে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের পূর্বপুরুষরা এ গ্রামে চলে আসেন বসবাস করবার জন্যে।
বাংলায় তখন ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য। এই সুযোগে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ করে যশোহর জেলায় নীলকুঠিয়াল সাহেবদের অবাধ অত্যাচারে বাংলার চাষি সম্প্রদায় মুমূর্ষুপ্রায়। কুঠিয়ালদের এই অত্যাচারের নিখুঁত চিত্র সাহিত্যে রূপায়িত করলেন নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁর নীলদর্পণ-এ। চাঞ্চল্য জাগল সারাদেশে। বাংলার অত্যাচারিত কৃষক-জনসাধারণের দুঃখদুর্দশার কথা স্মরণ করে তাদের দাবি জানাবার ভার গ্রহণ করলেন শিশিরকুমার। তিনি নিজের গ্রামের ক্ষুদ্র কুটির থেকে অমৃতবাজার পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন। পলুয়া-মাগুরার নূতন নামকরণ হল ‘অমৃতবাজার’! আমার জন্মভূমি অমৃতবাজার। জনসাধারণের মুখপত্ররূপে অমৃতবাজার পত্রিকার সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকাটিকে জাতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় স্থানান্তরিত করতে হল। কিন্তু বাংলার এক নিভৃত কোণে এই গ্রামে আজকের বিশ্ববিশ্রুত অমৃতবাজার পত্রিকার সূতিকাগৃহের প্রাচীন স্মৃতির সাক্ষ্য এখনও বর্তমান।
গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবহমান কপোতাক্ষ, তারই হাত ধরাধরি করে চলেছে চৌগাছা রোড। নদীর সমান্তরালে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে শিশিরকুমার দাঁতব্য চিকিৎসালয়, শ্ৰীশ্ৰীসিদ্ধেশ্বরী বাড়ি, হরিসভা-ভবন ইত্যাদি। মহাত্মা শিশিরকুমারের কৃতী সন্তান তুষারকান্তি ঘোষের প্রচেষ্টায় ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে এই দাঁতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হয় আর্ত দরিদ্র জনসাধারণের সেবার জন্যে। চিকিৎসালয়ের অনতিদূরেই পথিকদের তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে ‘পীযূষ পয়োধি। সকাল, সন্ধ্যায় সে সরোবরের ঘাটে গ্রামবাসীদের ভিড় জমে।
প্রকৃতির মায়া-মালঞ্চ অমৃতবাজার গ্রাম। কপোতাক্ষের বুকে দেশ-বিদেশের পণ্যসম্ভার নিয়ে মাঝিমাল্লারা সারি গেয়ে চলেছে ‘হেইয়ে হেরো, হেইয়ে হেয়োলগি ঠেলে গুড় বোঝাই দু-হাজার মনি নৌকা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। সুরটা কানে এসে বাজছে। চৌগাছা সড়ক দিয়ে গোরুর গাড়ি চলেছে ক্যাঁচক্যাঁচ। রাস্তার দু-ধারে শাল, সেগুন, তাল, কৃষ্ণচূড়া, নিম, নিশুন্দি গাছের সারি। পীযূষ-পয়োধির তীরে গন্ধরাজ, চামেলি, হেনা আর ভাঁটফুলের গন্ধে বিভোর হাওয়া-বাতাস।
দক্ষিণে ধু-ধু করে ধান-কড়াইয়ের খেত। দূরে দেখা যায় দেওয়ানগঞ্জ, ঝিকরগাছা বন্দর আর তার ঝুলন-সেতু। পূর্ব দিকে বিশাল বিল ‘ডাইয়া’। ডাইয়া’ বিল সত্য সত্যই দর্শনীয়। তার গভীর জলে মৎস্যকন্যার রূপকথার দেশ। যশুরে কইমাছও মেলে প্রচুর। শিকারিদের প্রমোদস্থান এ বিল। ধান পাকার প্রাক্কালে অসংখ্য পাহাড় আর সামুদ্রিক পাখি আসে ঝাঁকে ঝাঁকে। কলকাতা থেকে ফিরিঙ্গি শিকারিরা ও পক্ষী ব্যাবসায়ীরা বন্দুক ও ফাঁদ নিয়ে আসে শিকারে। সাদা-কালো-ধূসর তাঁবুতে ছেয়ে যায় গাঁয়ের আশপাশ। সাহেব শিকারিরা খুবই দিলদরিয়া। শিকার সন্ধানে এসে বেশ দু-পয়সা খরচা করে যায় তারা। গ্রামবাসীদেরও কিছু অর্থাগম হয় এই মরশুমে।
গ্রামের মধ্যে শ্রীশ্রীকালীমাতার একটি বিগ্রহ আছে। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস তিনি নাকি জাগ্রত। জাতিধর্মনির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান সকলকেই এই কালীমাতার কাছে পুজো দিতে দেখেছি। আগে নাকি এই পীঠস্থান কপোতাক্ষের কূলে অবস্থিত ছিল। কালের গতিতে ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তনের ফলে এই নদী বর্তমানে অনেকখানি পশ্চিম দিকে সরে গেছে।
বহু জাতের বাস এই গ্রামে। কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, ডাক্তার, কবিরাজ, কবিয়াল, লাঠিয়াল, কীর্তনীয়া, মৌলবি, পটুয়া, কোনো কিছুরই অভাব ছিল না। গ্রামটি বহু পাড়ায় বিভক্ত। হিন্দু পল্লিতে মজুমদার, বিশ্বাস, সেন, মিত্র, ঘোষ ইত্যাদি; বহু পাড়ার মতন মুসলমান পল্লিতেও কাজী, বেহারা, সর্দার, মোল্লা, পাঠান ইত্যাদি পাড়া রয়েছে। হিন্দু মুসলমানে কোনোদিন বিদ্বেষের ভাব ছিল না। হিন্দুর পুজো-পার্বণে, তার দুর্গোৎসবে, চড়ক পুজোয় মুসলমান ভাইরা অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। ভাই-ভাই রূপেই বাস করেছে তারা। একসঙ্গে মিলেমিশে কাজ করে হিন্দু-মুসলমান সকলেই গ্রামের উন্নতির জন্যে আত্মনিয়োগ করে এসেছে। হিন্দু চাষি ছিল মুসলমান চাষির দরদি ভাই, মুসলমানেরাও সুখে দুঃখে হিন্দুদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। গ্রামবাসী হিন্দু-মুসলমান দৃঢ়কণ্ঠে একটি সত্যই ঘোষণা করে এসেছে–
রাম রহিম না জুদা কর ভাই
দিলটা সাচ্চা রাখো জী।
কালচক্রে আজ রাম রহিম কী করে যে জুদা হয়ে গেল তাই ভাবি। মাটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত ছিল যে মানুষ, যে চাষি, তারা আজ কোথায়, কোন দেশে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়েছে কে জানে? এই গ্রামেরই কৃষাণ-বধূদের গান গাইতে শুনেছি–
মাটি আমার স্বামী-পুত,
মাটি আমার প্রাণ;
মাটির দৌলতে এবার
গড়িয়ে নিব কান।
এই চাষিদের জন্যে ধান বিলিয়ে দিতেন মহাজন মহেশ কুন্ডু। হিন্দু-মুসলমান কৃষক। সকলেই তাঁকে ডাকত ‘ধানিদাদা বলে।
পাশের গ্রাম ছুটিপুরে পুজোর সময় বসত মেলা। দূর-দূরান্তর থেকে গ্রামবাসীরা আসত এই মেলায়। বিজয়ার দিন নদীতে নৌকাবাইচ দেখতেও বহু দর্শনার্থীর সমাবেশ হত।
গ্রামে শখের যাত্রার দল ও নাট্য-সমিতি গঠিত হয়েছিল। পুজো-পার্বণে গ্রামবাসীদের আনন্দানুষ্ঠানের সময় এদের ডাক পড়ত।
গ্রামের উত্তরে পলুয়া মহম্মদপুর, মুসলমানপ্রধান গ্রাম। ধীরে ধীরে সে-গ্রামের অনেকেই এসে অমৃতবাজারে বসতি স্থাপন করেছিল। নদীর ওপারে ‘বোধখানা’ ও ‘গঙ্গানন্দপুর’। গঙ্গানন্দপুর একটি শিক্ষিত উন্নতিশীল গ্রাম। এ গ্রামের মদনমোহনের মন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
সব কিছু মিলিয়েই একটি সুন্দর গ্রাম অমৃতবাজার। এ গ্রামের নামাঙ্কিত সংবাদপত্র আজ বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে। তুলসীতলার প্রদীপের মৃদু আলোয় ঘেরা সেই গ্রাম তেমনই নীরবে নিভৃতে তার অধিবাসীদের মনে শান্তি ও আশা সঞ্চার করে আসছিল। গ্রাম নিয়েই তাদের সুখ, দুঃখের দিনে গ্রামই ছিল তাদের সান্ত্বনা। আমিও সেই হাজার হাজার গ্রামবাসীরই একজন। রাজনীতির পাকচক্রে কেমন করে যে সে-গ্রামকে ছেড়ে আসতে হল জানি না, জানলেও সে মর্মন্তুদ কাহিনি বর্ণনার ভাষা আমার নেই। গ্রাম ছাড়ব, একথা ভাবতে মন চায়নি। তবু ছেড়ে আসতে হল। বিদায়ের দিন তুলসীতলায়, ঠাকুরঘরে, এমনকী গোয়ালদোরে শেষপ্রণাম জানাল সবাই। বৃদ্ধা পিসিমা ঠাকুরঘরের দোর ছাড়তে চাইলেন না, পিসিমার চোখের জলে সজল ও করুণ মুহূর্তে আমারও মন ভিজে গেল। পূর্বপুরুষদের বহুস্মৃতিবিজড়িত যে গ্রাম আমার কাছে তীর্থস্বরূপ, সেই গ্রামজননীর উদ্দেশ্যে শেষসন্ধ্যায় একটি সশ্রদ্ধ প্রণাম রেখে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হলাম। পায়ে-হাঁটা পথে এগিয়ে চলেছি, মন পড়ে রয়েছে পেছনে। সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, তবু জন্মভূমির আশা লোপ পায়নি। মন বলছে, এ মেঘের অন্তরালেই রয়েছে সূর্যকরোজ্জ্বল উদার নীলাকাশ। কিন্তু সে-দিগন্ত আর কতদূর?
.
সিঙ্গিয়া
ছায়াচ্ছন্ন সমুদ্রের মতোই সীমান্ত-ছোঁয়া রাত্রির মায়া ঘনিয়ে আসে নিঃশব্দে। নিঃসীম নিস্তব্ধতা চারিদিকে–সৃষ্টি যেন নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছে অনাগতের অবগুণ্ঠন উন্মোচনের ব্যাকুলতা নিয়ে। প্রতীক্ষা-ক্লান্ত মুহূর্তগুলি আপনা হতেই ভারী হয়ে ওঠে। দিগন্তপ্রসারী এই অচঞ্চল স্তব্ধতার মাঝে, অন্ধকারের বুক চিরে পুরী এক্সপ্রেস ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে তীর্যক গতিতে–গোটা পৃথিবীর জীবন-শক্তিকে যেন ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে সে।
ধূলি ধূসর কাঁচের জানালার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে আছি বাইরে–কত গ্রাম, কত প্রান্তর, কত বনছায়া একে একে সরে যায় চোখের সমুখ দিয়ে, কিছুই দাগ কাটে না মনে। অজানা শঙ্কায়, দুর্নিবার সংশয়ে মন আন্দোলিত হতে থাকে। আজন্মের চেনা পরিবেশ ছেড়ে গৃহহারা আমরা বেরিয়েছি পথে–নতুন ঘরের সন্ধানে, ঠাঁই খুঁজে নিতে দেশ-দেশান্তরে। বাস্তুহারা জীবনে সুদূরের আহ্বান, চোখে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ছায়া–দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে।
সহসা আলোর শিখায় কাঁপন লাগে। স্টেশন অতিক্রমের সাংকেতিক ধ্বনি মুখর হয়ে ওঠে –শূন্য মন্দিরে বাঁশির তীক্ষ্ণ সুর বড়ো বেসুরে বাজে। গতির আনন্দ ভুলে যাই। পুঞ্জীভূত চিন্তারাশির জটলা জটিল হয়ে ওঠে। ভীরু মন পিছনপানে ফিরে চায় নিতান্তই অসহায়ের মতো।
বনানীর অন্তরালে অপসৃয়মান অচেনা গ্রামগুলির মতোই ফেলে-আসা জীবনের বিস্মৃত কাহিনি ছায়া ফেলে মনের পাতায়, সুখ-দুঃখের স্মৃতিবিজড়িত ছিন্ন-বন্ধন গ্রামখানি তাজা ফুলের হাসির মতোই ভেসে ওঠে চোখের তারায়। অতীতের পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যৎ ম্লান হয়ে আসে, একটা অনিশ্চয়তা মিয়মাণ করে তোলে মনকে–জীবনের জয় প্রতিষ্ঠার অহংকার নিষ্প্রভ হয়ে আসে।
আমাদের নতুন পরিচয়–এপারে শরণার্থী, ওপারে পরবাসী। স্বাধীনতার সৈনিকদের জীবনে এ এক মর্মান্তিক পরিহাস। শরণার্থী হিসাবে অনুকম্পার পাত্র হতে ঘৃণা জাগে, ব্যথা ঘনায় মনে। আর পরবাসী? সে-কথা ভাবতেও মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে–নিষ্ফল আক্রোশে গুমরে গুমরে মরে। স্বার্থোদ্ধত অবিচার বেদনাকে পরিহাস করে। প্রশ্ন জাগে, কেন এমন হয়?
সেদিনও তো দ্বন্দ্ব ছিল, কলহ ছিল, বিরোধ ছিল, কিন্তু পুঞ্জীভূত মালিন্য তো আবহাওয়াকে এমন বিষিয়ে তোলেনি, এমন অব্যক্ত বেদনার সৃষ্টি করেনি। স্বার্থে স্বার্থে অপরিহার্য সংঘাত কোনোদিন যৌথ পরিবারের পারিপার্শ্বিকতা অতিক্রম করেনি। বিরোধ বিসংবাদে আত্মীয়তার সীমা লঙ্ঘিত হয়নি। বাংলার আর পাঁচখানা গ্রামের মতোই আমাদের গ্রামেও হিন্দু-মুসলমান পরস্পরকে আপন জেনে সদ্ভাবে বসবাস করেছে। শরতের স্বচ্ছ আকাশে কাজলকালো মেঘের আবিলতা স্থায়ী হতে পারে নি–ক্ষণিকের বর্ষণেই মলিনতা ধুয়ে গেছে।
খরস্রোতা ‘চিত্রা’ ও ‘নবগঙ্গা’র মোহনায় যশোহরের বিশিষ্ট ব্যাবসাকেন্দ্র নলদির প্রান্তবর্তী আমাদের এই ছায়া-ঢাকা গ্রামখানি, প্রকৃতির মায়া-মালঞ্চ যেন। বাইরে থেকে বোঝাই যায় না –ঘরবাড়ি আছে, রাস্তাঘাট আছে, না হাজার লোকের বসতি আছে। কবে কোন এক অজ্ঞাত প্রভাতে কে যে এর নাম দিয়েছিল ‘সিঙ্গা’ সে-কথা কেউ মনে করতে পারে না। ব্রিটিশ আমলে ডাকঘর প্রতিষ্ঠাকালে গ্রামের নতুন নামকরণ হল ‘সিঙ্গিয়া’, এই কথাই শুধু মনে পড়ে।
সবুজ স্নিগ্ধ গ্রামখানির সারাঅঙ্গে অপূর্ব শ্যামলিমা। নিত্যকালের অতিথির মতোই ‘বারোমাসে তেরো পার্বণ’ এই পল্লিরও মধুর আকর্ষণ।
এইসব উৎসবে আনন্দে হিন্দু-মুসলমান সমভাবেই অংশগ্রহণ করেছে–মেলায়, নৌকাবাইচে, ঘোড়-দৌড়ে, গোরু-দৌড়ের তীব্র প্রতিযোগিতায় সে কী উদ্দীপনা! সেই আনন্দ গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনকে সাময়িকভাবে হলেও মুখর করে তুলেছে। আবার কখন গভীর রাতে ধানখেতের কিনারে দেখা গেছে অসংখ্য টিমটিমে আলো–আলেয়ার আলোর মতো কখনো স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে, কখনো-বা ধানের শিষের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায়। কাছে গিয়ে অবাক হয়ে দেখতে হয়, হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে কোঁচ দিয়ে মাছ মেরে চলেছে। আলোয় মাছ মারার এই মরশুমেও মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কত নিবিড় তারই পরিচয় প্রতিভাত হয়েছে। অনেক উঁচু ওই আকাশ, চাঁদ-সূর্য হাত ধরাধরি করে সেদিন সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছে।
এই সেদিনের কথা। চারজন মুসলমান আসামি, নারী নিগ্রহের দায়ে অভিযুক্ত। মিত্রবাবুদের সদর কাছারিতে বিচার শুরু হয়েছে। গ্রামের লোক ভেঙে এসে কাছারি বাড়ির বিস্তীর্ণ অঙ্গনে ভিড় জমিয়েছে। হিন্দুর কাছারিবাড়িতে বিচার, বিচারকদের মধ্যে আছেন বাবুরা ছাড়া কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মাতব্বর মুসলমান। কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হল। আসামিরা নির্বিবাদে শাস্তি মাথা পেতে নিলে। পুলিশ নেই, আদালত নেই, দন্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নেই, নেই। কোনো কেলাহল। সুস্থ পরিবেশে সুষ্ঠু ব্যবস্থা। কঠোর দন্ডাজ্ঞার মধ্যে ভবিষ্যৎ প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর পরিস্ফুট হয়ে উঠল। অপরাধীর শাস্তি দিতে উভয় সমাজকেই একযোগে এগিয়ে আসতে দেখেছি সেদিন।
এই ঘটনার কিছুদিন পরেই গো-হত্যার ব্যাপারেও অনুরূপ ব্যবস্থায় বিচারসভা বসতে এবং গ্রাম্য পঞ্চায়েতের কঠোর সিদ্ধান্ত নির্মমভাবে প্রযুক্ত হতেও দেখেছি। তথাপি ধর্মের জিগির ওঠেনি, ধর্মের নামে জোট-পাকানোর কথা কেউ ভাবেনি। স্বাভাবিক জীবনধারায় ব্যতিক্রম সৃষ্টি শাস্তিবিধানের যোগ্য বলেই বিবেচিত হয়েছে।
মাস্টার সাহেবের পাঠশালাতেই বা না পড়েছে কে? পরবর্তী জীবনে যাঁরা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, বিশ্বের জ্ঞানভান্ডার হতে আহরণ করে যাঁরা সমাজে মর্যাদার আসন লাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে এমন কে আছেন যিনি মৌলবি আব্দুল বিশ্বাসের পাঠশালায় হাতে খড়ি দেননি এবং মাস্টার সাহেবের শাসানি, চোখরাঙানি ও চাবুক সহ্য করেননি। শণের মতো সাদা একগাল দাড়ি, দারিদ্র্যের কুঞ্চিত রেখা সর্ব অবয়বে, সৌম্য মূর্তি মাস্টার সাহেব। বড়ো ঘরের ছেলেদেরও তাঁর কাছে পাঠ নিতে আটকায়নি, শাস্তি গ্রহণেও অমর্যাদা হয়নি। একটানা জীবনস্রোতে কখনো বিস্ময়কর ছন্দপতন ঘটেনি।
‘ছুটি বঁটি দিয়ে কুটি’ হাঁক দিতে দিতে ছেলের দল ছুটির পর মাঠে এসে নেমেছে। ‘হাডুডু’, ‘বুড়ি-ছোঁয়া’, ‘কানামাছি’ প্রভৃতি নিভাঁজ গ্রাম্য খেলাধুলোর মধ্যে কিশোর জীবনে যে অনাবিল আনন্দের সঞ্চার হয়েছে, সে-আনন্দের অংশ থেকে মিনু, হারান, ভোলাদার সঙ্গে আজিজ, করিমও বাদ পড়েনি। খেলার মাঝে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ দেখিনি, বিত্তশালী ও বিত্তহীনের প্রশ্ন ওঠেনি। কিন্তু কখনোই কি কোনো গোলযোগ বাধেনি? খেলায় হারজিত নিয়ে মারপিট পর্যন্ত হতেও দেখেছি, কিন্তু মাস্টার সাহেবকে ডিঙিয়ে অভিযোগ অভিভাবকের কানে কোনোদিন পৌঁছাতে পারেনি। আজও তো সেই গ্রামই আছে।
এই তো সেই গ্রাম, যেখানে একটি পল্লি-পাঠাগারকে কেন্দ্র করে একদিন রাজনৈতিক চেতনা গ্রাম হতে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল।
কলেজের ছাত্র ‘কালোদা’ সেবার পুজোর ছুটিতে বাড়ি এসে সকলকে কাছে ডেকে বোঝালেন, ক্লাসের পড়াই সব নয় রে, জীবনে বড়ো হতে হলে চাই মনীষা, চাই জ্ঞানার্জনের নেশা। এই লক্ষ্যের পথে গ্রন্থাগার যে অপরিহার্য, সে-সম্বন্ধে তাঁর কথায় নিঃসংশয় হয়ে ছেলের দল আমরা মেতে উঠলাম লাইব্রেরি গড়ে তুলতে। ‘বিবেক লাইব্রেরি’ ভূমিষ্ঠ হল। মুখ্যত স্বামীজির গ্রন্থাবলি আর স্মরণীয় যাঁরা তাঁদের কয়েকজনের জীবনী নিয়ে গ্রন্থাগারের উদবোধন হল। কিশলয় অঙ্কুরিত হল, ক্রমে ক্রমে কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে যেদিন পা দিল সেদিন থেকে এই সাংস্কৃতিক কেন্দ্রকে অবলম্বন করে রাজনৈতিক চক্র গড়ে উঠতে লাগল। মহাত্মাজির অসহযোগ আন্দোলন কিংবা অগ্নিযুগের আত্মাহুতির আহ্বান কোনোটাই বাদ পড়েনি গ্রাম্য জীবনে প্রতিফলিত হতে–প্রান্তবর্তী এই গ্রামখানির সঙ্গে আশপাশের গ্রামগুলিকেও আলোড়িত করতে। সেদিনের সেই জাতীয় আন্দোলনকে পুষ্ট করতে, প্রেরণা দিতে এই পল্লি-পাঠাগারের অবদান যে কতখানি, তার হিসাব আজ আর কে করবে?
পুলিশ সাহেব এলিসন ও পূর্ণ দারোগা নির্বিচারে তল্লাশি, গ্রেপ্তার, গৃহদাহ ও লুণ্ঠন চালিয়েও জনতার কণ্ঠ রুদ্ধ করতে পারেনি, কংগ্রেস ভবনটিকে পুড়িয়ে দিয়েও গ্রামের মানুষের মন থেকে কংগ্রেসকে নির্বাসিত করতে পারেনি। বিপ্লবী সন্দেহে এগারো জন যুবককে যেদিন একসঙ্গে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গ্রামের সকলে সেদিন রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করে তার প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ভিতর বাড়ির অঙ্গন ও নদীর ঘাটের বাইরে যাদের কোনো পরিচয় নেই, সেইসব পুরললনারাও সেদিন রাস্তায় নেমে এসেছিলেন ধৃত তরুণদের অভিনন্দন জানাতে। স্বতঃস্ফূর্ত হরতালে মুসলমান সমাজও যোগ দিতে এগিয়ে এসেছিল। নারী-পুরুষের মিলিত কণ্ঠে বন্দেমাতরম ধ্বনির মধ্যে বন্দিদের নিয়ে পুলিশ সাহেবের লঞ্চ ছেড়ে গেল। জাতীয় ধ্বনির মধ্যে জনতার প্রতিবাদ ও রুদ্ধ আক্রোশ ফেটে পড়তে লাগল। লঞ্চ চলে গেল। নদীর এপারে-ওপারে তখনও গাঁয়ের লোকের ভিড়, চোখে তাদের প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ।
গ্রন্থাগারের সঙ্গে সঙ্গে ব্যায়ামাগারও গড়ে উঠতে থাকে। শরীরচর্চায় এমনই অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় যে, খেলার মাঠে লোক-অভাব বিস্ময়ের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। যে-খেলা তরঙ্গ তোলে মনে, সেই ফুটবল, ক্রিকেট থেকে লাঠিখেলা, ছোরাখেলার আকর্ষণ প্রবল হয়ে ওঠে। গ্রাম হতে গ্রামান্তরে আন্দোলনের ঢেউ গিয়ে লাগে। জোয়ান ছেলে জোর কদমে চলে অটুট সংকল্প নিয়ে।
প্রবীণদের ও মধ্যবয়স্কদের আড্ডা বসে বসুবাটিতে, রাজকাছারিতে, আর মিত্রবাবুদের বৈঠকখানা ঘরে। দু-মাইল দীর্ঘ গ্রামখানির অধিকাংশ লোক জমাজমির ওপর নির্ভরশীল, অভাবের তাড়না নেই তেমন। তা ছাড়া সম্পন্ন পরিবারের যারা, আড্ডা জমাতে তাদেরই উৎসাহ বেশি। তাস, পাশা ও দাবাকে ভর করে নৈশ আড্ডা জমে ওঠে। এই আড্ডার আনুষঙ্গিক পান-তামাক এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে চা। রাত্রি আটটায় গ্রাম যখন ঘুমোয়, এদের খেলার আসর সবে তখন জমে ওঠে। রাত্রি বারোটায় সুপ্তিমগ্ন গ্রামের জনবিরল পথে যে যার গৃহের পানে চলে। ডরে আশঙ্কায় কেউ বা হাততালি দেয়, কেউ বা লাঠি ঠক-ঠক করে চলে। আর বলে দস্যি ছেলেদের হাতের কোদাল পড়ে বর্ষা-বোয়া গ্রামের দুর্গম পথও এমনই সুগম হয়েছে যে, চোখ বুজে চলতেও বাধা নেই আর। সোয়াস্তিতে চলে আর আশীর্বাদ করে মনে মনে।
পথের প্রান্তে চালাঘরের মধ্যে লণ্ঠন জ্বালিয়ে শখের যাত্রার মহড়া চলে। নারীকন্ঠের ব্যর্থ অনুকরণে পুরুষের কর্কশ স্বর, অন্ধকারের বুকে আছড়ে পড়তে থাকে। হারমোনিয়ামের চড়া আওয়াজ নিশুতি রাতের স্তব্ধতাকে ব্যঙ্গ করে মাঝে মাঝে, আকাশে তারার মালা তখনও মিটমিট করে।
গ্রামের ছেলেরা প্রতিবছর দলে দলে পড়তে যায় পার্শ্ববর্তী শহরের স্কুলে। লজিং-এর অথবা বোর্ডিং-এ আশ্রয় খুঁজে নিতে হয়। তবু গ্রামে হাই স্কুল গড়ে ওঠে না। চাষি প্রজারা ইংরেজি লেখা পড়া শিখলে বাবুদের মান্য করবে না, এই আশঙ্কাতেই নাকি গ্রামের কর্তারা গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠায় বাদী হন–সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশকেও হার মানিয়ে ছাড়েন। কেরানির অভাব পূরণের জন্যে একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব্রিটিশকে একদিন বাধ্য হয়েই ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তন করতে হয়েছিল। এঁদের তো সে বালাই নেই। উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যা হলেই নায়েব গোমস্তার কাজ আটকায় না। তাই স্কুল স্থাপনের প্রয়াস কয়েকবারই ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু কৃতী ছেলেরা সেবার ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি সামনে রেখে কাজে নেমে গেল। প্রধানশিক্ষক বাইরে থেকে এলেন, বহুজনের সমবেত চেষ্টায় স্কুল গড়ে উঠল। যথাসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনও পাওয়া গেল। দুই শতাধিক ছাত্র প্রতিষ্ঠানটির পাকা ভিত গড়ে তুলল। চালু প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক নিয়মেই চলতে লাগল। কর্তারা বললেন, এইবার গ্রাম গেল, মানীর মান সম্ভ্রম বিপন্ন হল। কিন্তু সেদিনও গ্রাম যায়নি। বিদ্যাপীঠ পল্লবিত হয়ে জীবন্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। সম্ভম কিন্তু তখনও বিপন্ন হয়নি, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র রচিত হয়ে জীবনের জয় সূচিত হল। নীল আকাশের আস্তরণের নীচে আজও স্কুল ভবনটি তেমনই আছে। সেইসব শিক্ষক আজ আর নেই, যাঁরা ত্যাগের আদর্শকে ছাত্রদের সামনে তুলে ধরেছিলেন, আর সেইসব ছাত্রও নেই যাঁরা আর্তের সেবায় বিপদের ঝুঁকি নিতে অকুণ্ঠিত ছিলেন। আর সবই আছে, নেই শুধু প্রাণের স্পন্দন।
জেলাবোর্ডের রাস্তাটি আজও এইভাবে গ্রাম ও বিলের স্বতন্ত্র সত্তার সাক্ষ্য হয়ে আছে। আজও এই পথে দেশ-দেশান্তরের লোক যাতায়াত করে; গ্রামের লোক বাজারে যায়, ডাকঘরে যায়, স্টিমার ঘাটে যায় এই পথে। কিন্তু সংকীর্তনের দল আর বেরোয় না, শিবের গাজন এ পথে চলে না।
শারদোৎসবে, চড়ক মেলায়, কালীপুজোয় ও হোলিখেলায় যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণ-বন্যা গ্রামখানাকে প্লাবিত করে দিত, বাজি-বাজনায়, সাজে-সজ্জায়, আমন্ত্রণে-নিমন্ত্রণে যে প্রাণের পরিচয় প্রত্যক্ষ হয়ে উঠত, আজ তা অলীক কাহিনি।
ছেড়ে-আসা গ্রামের ছায়াশীতল ঘরের মায়া নিত্যপিছন টানে, তবু চলতে হয় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের পথে। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে দৃষ্টিকে ঝাপসা করে দেয়। পারিপার্শ্বিক ভুলে যাই, মনের গভীরে জাগে–মাটি চাই, ঠাঁই চাই, জীবনের বিকাশের পথ উন্মুক্ত পেতে চাই।
ট্রেনের গতি আবার স্তব্ধ হয়ে আসে। চোখ-ঝলসানো আলো এসে চোখে লাগে। বড়ো স্টেশন–বালেশ্বর। অগ্নিযুগের রোমাঞ্চময় স্মৃতি বিজড়িত এর সাথে। বিপ্লবের পূজারির ঐতিহাসিক বীরগাথা সহসাই প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে–চলচ্চিত্রের মতোই ছায়া ফেলে যায় মনে। অমাবস্যার অন্ধকারের পারে একফালি চাঁদ চিকচিক করে ওঠে। বাঙালি বীরের বিপ্লবসাধনার তীর্থপীঠ বালেশ্বরে দাঁড়িয়ে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের স্বপ্ন জাগে চোখে। ভরসা জাগে, অনাগত ভবিষ্যতে পূর্বাঞ্চলের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে মানুষের শবদেহের সারে অঙ্কুরিত হবে নবীন শস্য। বিপ্লবের বহ্নিশিখায় পূর্ণ হবে আবর্তন।
রংপুর – হরিদেবপুর
মন বলে, যাই। অনেকদিন স্বপ্নেও দেখেছি। ভাবতে ভাবতে চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় বৃদ্ধ ছুতোর মথুর কাকা। খোল-বাজিয়ে কানাইদার মিষ্টি গলার গান শুনতে পাই যেন। বৃদ্ধ আফসর দাদু এসে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়ান। উতলা হয়ে ওঠে মন। মনে মনেই ফিরে যাই উত্তর বাংলার সেই লোক-না-জানা অজ্ঞাত গ্রামে, আমার জন্মভূমিতে।
উত্তরবঙ্গের রংপুর টাউন থেকে মাত্র বারো মাইল দূরে আমাদের ছোট্ট গ্রাম, হরিদেবপুর। তার কোল দিয়ে বিনুনির মতো এঁকে-বেঁকে চলে গেছে শঙ্খমারী নদী। ছোট্ট নদী-খোলা তরোয়ালের মতোই চকচকে ছোট্ট নদী। বর্ষাকালে সে কিন্তু আর ছোট্টটি থাকে না। অবাধ্য সন্তানের মতো উদ্দাম স্রোতে সে ভাসিয়ে দিয়ে যায় তার দুটি পাড়। ধান আর পাটগাছের গুঁড়িতে দিয়ে যায় তার পেলব মাটির স্পর্শ। আকারে ক্ষুদ্র পালতোলা নৌকোর-সারি ভেসে বেড়ায় দুরন্ত বালকদলের মতো। প্রতিদিন দল বেঁধে আমরা স্নান করতাম। পাড়ের ওপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়াতে কত না আনন্দ পেতাম সেদিন। সবচেয়ে ওস্তাদ ছিল পাড়ার নেপাল মামা। একাদিক্রমে তিন-শো বার ডুব দেওয়াই ছিল তাঁর স্নানের বিশেষত্ব। একহাতে নাক ধরে তাঁর ডুব শুরু হত–উঠে আসতেন জবাফুলের মতো টকটকে লাল চোখ-জোড়া নিয়ে। জ্বর তাঁর কিন্তু কোনোদিন হয়নি সেজন্যে।
আগেই বলেছি গ্রামটি খুব ছোটো। মোট কুড়ি-একুশ ঘর হিন্দু আমরা, আমাদের পাড়ার নাম কায়েত পাড়া। সামনে ও পেছনে মুসলমান পাড়া, নয়া পাড়া আর পাছ পাড়া–সব মিলে হরিদেবপুর।
গ্রামের নয়াবাড়ি অর্থাৎ ঘোষমশাইদের বাড়িতে গড়ে উঠেছিল একটি সমিতি–সৎসঙ্গের আদর্শে। বিপ্লবী যুগে এই সঙ্ঘের দান বড়ো কম নয়। পাড়ার সবার সুরেশকাকা ছিলেন আমারই কাকা। তিনি ছিলেন সমিতির নেতা। জ্ঞান হওয়ার পর দেখেছি প্রায়ই আমাদের বাড়ি সার্চ হত। পাটের গুদাম লন্ডভন্ড করে দিয়ে যেত পুলিশ!
কোনো একদিন সার্চ করতে এসে পুলিশ যাওয়ার বেলায় ধরে নিয়ে গেল সুরেশকাকা আর সামসুদ্দিনদাকে। সামসুদ্দিনদা পাছ পাড়ার বুড়ো আফসর দাদুর একমাত্র ছেলে। সেদিন আফসরদাদুকে দেখেছি তামাক খেতের আলের ওপর দাঁড়িয়ে এই বিপ্লবীদ্বয়কে বিদায় দিতে। বিদায় দিতে দেখেছি হাসিমুখে তাঁর প্রাণের ছেলে সামসুদ্দিনদাকে। তাঁরা জেলে গেলেন কিন্তু ফিরে এসেছিলেন পাঁচ বছর পর।
সেই বিপ্লবী সুরেশকাকা এবার সাতপুরুষের ভিটে ত্যাগ করে আসবার সময় আমাদের তকতকে উঠোনের মাটি মাথায় নিয়ে, চোখের জলে মাটি-মায়ের বুক ভিজিয়ে দিয়ে চলে এসেছেন এ প্রান্তে।
আমরা চলে যাচ্ছি এ খবর পেয়ে সামসুদ্দিনদার সত্তর বছরের বুড়ো বাবা আফসর দাদু লাঠিতে ভর দিয়ে পথের মাঝে সুরেশকাকার হাত ধরে বললেন, ‘দ্যাশ ছাড়ি তোরা কোটে যাওছেন দেবমশাই। তোরা চলি গেইলে আমরা গুলা কেমতি করি বাঁচিম। তোর চোখ পানি! কিন্তু বাস্তবের রূঢ় আঘাতে সেই স্নেহশীল বুড়ো মুসলমান প্রতিবেশীর আকুল আবেদন উপেক্ষা করেই স্বপ্ন দিয়ে গড়া সেই ছোট্ট গ্রামখানিকে ছেড়ে আসতে হয়েছে। আমাদের সবাকেই– সুরেশকাকাকেও।
জেল থেকে ফেরার মাস তিনেক পরে একদিন সন্ধ্যায় পল্লিমায়ের দুরন্ত ছেলে সামসুদ্দিনদা মায়ের ওই ছায়াঘন কোলের ওপরে ঘুমিয়ে পড়লেন চিরদিনের মতো। স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল আমাদের ছোট্ট গ্রামটি। মাঝিপাড়ার বাজার সেদিন বসেনি…খেতে সেদিন কেউ নিড়ানি দিতে যায়নি…। শঙ্খমারীর কোলের বড়োপুরোনো অশ্বত্থ গাছটার তলায় আজও তিনি ঘুমিয়ে আছেন।
গ্রামের প্রধান খেলা ছিল হাডু-ডু-ডু আর ফুটবল। কালাচাঁদের মাঠে খেলা হত। সেই রোমাঞ্চময় রক্তরাগোজ্জ্বল অপরাহ্নের কথা ভুলিনি আজও। আজও ভুলিনি খোঁড়া জসিমের খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাডু-ডু-ডু খেলার দম দেওয়া। মহানগরীর সাতমহল বাড়ি ডিঙিয়ে, কত শত নদ-নদী-প্রান্তর পেরিয়ে, কত সবুজ ধানের খেত মাড়িয়ে আজও ভেসে আসে সেই ‘হাডু-ডু ড’ ধ্বনি।
শঙ্খমারীর তীরে ছিল আর একটা অশ্বথ গাছ। ঘন পত্রাবৃত ডালগুলো কিছুটা ঝুলে পড়েছিল শঙ্খমারীর জলের ওপরে হুমড়ি খেয়ে–চলতি জলে বাধা দিত তার এক-একটি পাতা–এক-একটি পচে যাওয়া ডাল। স্রোত কাটার শব্দ ভেসে আসত নদীর ছায়াঘন কূল থেকে। এই ছায়াতে মাঝে মাঝেই উদয় হতেন এক সাধু। এসেই কুড়িয়ে আনা কাষ্ঠফলকে জ্বালিয়ে দিতেন আগুন। সারাগাঁয়ের হিন্দু-মুসলমান ভাগ্য-জিজ্ঞাসা নিয়ে জড়ো হত সেই ভয়াল অন্ধকার ঘেরা অশ্বথ গাছের নীচের আলোয়।
বকুলতলা আমাদের খেয়াঘাট। বৈকালিক ভ্রমণস্থলও বটে। ছেলে-বুড়ো সবাই বেড়াতে আসত সেখানে। কেনী ঝালো, নিতাই মন্ডল, জুয়েন খাঁ–এরা তাদের ছোট্ট ছোট্ট ডিঙি দিয়ে নামমাত্র পারানি নিয়ে পার করে দিত শঙ্খমারী। শহর ফেরত যারা, তারা খবর বহন করে আনত সমস্ত জগতের। সত্যি-মিথ্যে মেশানো খবর… সিঙ্গাপুর পতনের সাতদিন আগে আমরা খবর পেয়েছিলাম জাপান সিঙ্গাপুরে হেরে গেছে। ভজু করমজায়ীর দোকানটাই ছিল ছেলে-বুড়ো সবার আড্ডাস্থল। আকর্ষণ ছিল বইকী তার একটা। ভজু কিছুদিন হল শহর থেকে সওদা নিয়ে আসবার সময় একখানা করে খবরের কাগজ নিয়ে আসত। গ্রামের বিজয় ডাক্তার (হোমিয়োপ্যাথ) পড়তেন, আমরা সবাই শুনতাম। সে যেন একটি ছোটোখাটো সভা। ভজুর এতে কোনো আপত্তি হত না বরং তার দোকানের বিক্রি–সিগ্রেটটা, এটা-সেটা সেই সময়েই বেশি বিক্রি হত।
এই সেদিনের কথা। সেদিন খুব কুয়াশা পড়েছে সকাল থেকে। দেশি কথায় হাত পা সমস্ত ‘ট্যালকা হয়ে পড়েছিল। তবুও সন্ধ্যেবেলাটায় কিছুতেই বাড়িতে বসে সোয়াস্তি পেলাম না। চাদরটা জড়িয়ে নিয়ে গিয়ে উঠলাম সেই করমজায়ীর চালা ঘরটাতে। একে মেঘলা দিন তার ওপর একটা ঝাঁপ বন্ধ করে রাখায় ঘরটা আধার আধার হয়ে ছিল। ঘরে ঢুকে প্রথমে বিজয় ডাক্তারকে দেখতে পেলাম। ভজু করমজায়ী টাউন থেকে ফেরেনি তখনও, সবাই অপেক্ষা করছে তার জন্যে।
‘ভজুটি আছে না,কোন্টে গেইল?’–পাঁচপাড়ার তফি শেখ প্রশ্ন করে।
‘আরে নয় নয় বাহে, বেলা দুইট্যাৎ টাউনৎ গেইচে। এলায় ত ফিরবার কতা।’
‘আর ফিরোচে বাহে–আইজ আর’…কাজিমুদ্দিনের কথা শেষ না হতেই ঘরে ঢুকল ভজু। হাতে খবরের কাগজ, সওদাপত্র কিছুই নেই।
ডাক্তার আশ্চর্য হয়ে বললেন—’আরে এ ভজু, তুই সদাপত্তর কিছু করিসনি!’
ভজু কাগজটা এগিয়ে দিয়ে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল।
ডাক্তার কাগজখানা খুলে বসলেন। আমি দূরে দাঁড়িয়ে আছি। ডাক্তার চুপ করে কাগজ খুলে বসেই রইলেন। সবাই জোরে জোরে পড়তে বলল।
‘আর কী পড়ব ভাই–আবার গন্ডগোল। ডাক্তার হতাশভাবে উত্তর দিলেন।
‘আরে বাহে, কেটে গন্ডগোল হইল কন কেনে।’–তফি শেখ বলে।
‘সান্তাহারে গাড়িতে বহুৎ হিন্দু নিহত হইছে।’–ভজু যোগ দিল।–টাউন থেকে সব । হিন্দু গাড়ি বোঝাই হয়ে হিন্দুস্থানে যাচ্ছে এবং তারাও যাবে, একথাই ভজু বলতে যাচ্ছিল।
ভজুর কথা শেষ না হতেই কাজিমুদ্দিনের গলা উঁচু হয়ে উঠল—’তোরা কেটে যাবি? হামরা কি তোর জান মারি ফেলছি?’
কাজিমুদ্দিনের মতো মুসলমান ছিল বলেই আজ বেঁচে আছি–নইলে সেদিন ভজুর দোকান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় তফি শেখের মুখের চেহারা আজও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।
আমার গাঁয়ের সাধারণ মানুষের গলায় ভাওয়াইয়া গানের সুর মনকে মাতিয়ে তুলত। কথা-প্রাণ বাংলা গান। ভাওয়াইয়া গানের বেলাও তাই। একটি গানের কথা স্পষ্ট মনে পড়ছে। দোতারা বাজিয়ে তাল দিয়ে দিয়ে গান গাইছে ভাবুক,
ও আমার সাধের দোতারা, তুই যেন আমার মান রাখিস,
আমি রুপো দিয়ে তোর কান বাঁধিয়ে দেব!
অল্প বয়সে দোতারার আকর্ষণে পাগল হয়ে সংসার ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে ভাবুক। বাপ, ভাই, গ্রামের লোক কারুর কথাই সে কানে তোলেনি। গ্রামবাসীরা বিরোধী হয়ে দারোগাকে জানিয়ে দিয়ে তাকে হাতকড়া পর্যন্ত লাগিয়েছে। তবু সে দোতারা ছাড়েনি। সেই দোতারাকেই সে বলছে, ও আমার দোতারা, তুই যেন আমার মান রাখিস, আমি রুপো দিয়ে তোর কান বাঁধিয়ে দেব। অর্থাৎ সংসারে মোহগর্তে আর যেন তাকে প্রবেশ করতে না হয়, সে মান যেন তার থাকে। সত্যি কী উচ্চভাবের গান! আজ অবশ্য আমরা কমবেশি সবাই ভগ্ন-সংসার নিরুদ্দেশের পথের মানুষ। কিন্তু যেখানেই থাকি না কেন, আমার সোনার গ্রামখানি আমার চোখের সামনে।
পুজো এসে গেছে। আমাদের বারোয়ারি বাগানের বাঁধানো বেদি এবার খাঁ খাঁ করবে বিসর্জনের প্রদীপও জ্বলবে না। নদীর ঘাটে বিসর্জনের দিনের মেলায় সে কী কোলাহল হত! হিন্দু-মুসলমান সকলকে মিলনের রাখি পরিয়ে দেওয়া হত মেলায় প্রতি বছর। এবার হয়তো শুধু একটুকরো দক্ষিণা বাতাস বয়ে যাচ্ছে হু-হুঁ করে পল্লিমায়ের চাপা কান্নার সুরে। ধান মাড়াইয়ের স্বপ্নে কৃষকদের মন এবারও আনন্দে হয়তো ভরে উঠবে। কিন্তু মথুর কাকা আর কানাইদার মিষ্টি গলার কীর্তন আর এবারের কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোকে মহিমান্বিত করবে না। কালীপুজোর প্রসাদ বিলির আনন্দও আর উপভোগ করবে না কেউ। সব আনন্দই গেছে আমার গ্রামকে ছেড়ে। নইলে, পুজোয়, কালীপুজোয় যেসব থিয়েটার হত বারোয়ারি তলায়, সেগুলো তো এখানেই পেতে পারি–কিন্তু পল্লিমায়ের অদৃশ্য সেই স্নেহের টান তো পাব না আর।
রাজসাহী – হাজরা নাটোর তালন্দ বীরকুৎসা
বর্ষা নেমেছে চলনবিলের বুকে। জলে টইটম্বুর। যতদূর চোখ যায় জলে জলময়। শালুক ফুলে বিল যায় ভরে। সকালের কাঁচা রোদ সস্নেহে চুম্বন দিয়ে যায় উত্তর বাংলার এই গ্রাম হাজরা নাটোরের ধূলিকণায়। রাঙা মাটির দেশ এই বরেন্দ্রভূমি। প্রাতঃস্মরণীয়া রানি ভবানীর দেশ এই নাটোর। আজকের দিনে শিল্পীমন এই নাটোরেই হয়তো বনলতা সেনকে খুঁজে পেয়েছেন। সব কিছু মিলিয়ে এ গ্রাম আমার স্মৃতির সবটুকু জড়িয়ে আছে। আজ দেখছি ছেড়ে-আসা গ্রামের কাহিনির মধ্য দিয়ে হাজার বছরের বাংলার গ্রাম কথা কয়ে উঠেছে। জেগে উঠেছে দীর্ঘদিনের সুষুপ্তি থেকে। সে-কাহিনি শুনে মন ভরে যায়। বাংলার মূক মাটি এমন করে মুখর হয়ে ওঠেনি কোনোদিন। হাঁসুলী বাঁকের উপকথার মতোই পদ্মা মেঘনা আর চলনবিলের তীরের বাসিন্দারা নতুন ইতিবৃত্ত বলতে শুরু করেছে। সে-কাহিনির অনন্ত মিছিলে আমার গ্রাম নাটোরও একান্তে মিশে যায়।
শৈশবের কথা মনে পড়ে। নাটোরের আকাশে শীত ঘনিয়ে আসে। কাকলিমুখর শীতের ভোরবেলাটায় উঠি উঠি করেও মা-র কোল ছেড়ে কিছুতেই উঠতে ইচ্ছে করত না। বাগানের শিউলিতলায় একরাশ সাদা ফুলের গন্ধ কেমন করে জানি টের পেতুম। সেই ভোরে হরিদাসী বোষ্টমি করতাল বাজিয়ে বাড়ির দুয়ারে দুয়ারে হরিনাম কীর্তন করে সকলকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলত। হরিদাসী বোষ্টমির সুরেলা কণ্ঠের সে-গান আজও ভুলতে পারি না—
আর নিশি নাই ওঠ রে কানাই,
গোঠে যেতে হবে–দ্বারে দাঁড়ায়ে বলাই।
সে-গানের শব্দ অনেক দূর থেকে ভেসে আসত। আর বিছানায় থাকা সম্ভব হত না। কাঠবাদাম আর ফুল কুড়োবার লোভে খুব শীতের মধ্যেও উঠে পড়তাম। বাড়ির পাশেই জমিদারদের বাগানবাড়ি। সে-বাগানে সবরকম ফলের গাছই ছিল। উদ্যান-বিলাসী জমিদারবাবুরা বংশানুক্রমে এ বাগানে নানারকম ফলের গাছ পুঁতেছিলেন। আমাদের কৈশোরের দৌরাত্মময় রোমাঞ্চকর দিনগুলো অতিবাহিত হত সে-বাগানের গাছে গাছে। সেজন্যে যে কতদিন বাগানের মালির হাতে তাড়া খেয়েছি তার ইয়ত্তা নেই। গ্রীষ্মের দুপুরে চারধার যখন নিঃসাড় নিঝুম হয়ে যেত, মধ্যাহ্নের অলসতায় দ্বাররক্ষী তন্দ্রারত, সেই অবসরে পাঁচিল টপকে গাছে গিয়ে উঠতাম। এমনই করে প্রতিদিন গাছগুলোকে তছনছ করে চলে আসতাম আমরা; আরেকটি বিশেষ আনন্দের দিন ছিল, শ্রীপঞ্চমীর পুজোর দিনটি। শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই মন ওই দিনটির জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকত। সরস্বতী পুজো এলেই গ্রামের তরুণদের মন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠত। পুজোর আগেই সারারাত খেটে পুজোর আটচালা মন্ডপ তৈরি করতাম, গেট সাজাতাম। সব কাজের শেষে মধ্যরাত্রির অন্ধকারে চুপি চুপি খেজুরের ভাঁড় নামিয়ে রস চুরি করার মধ্যে যে-রোমাঞ্চ ছিল তা আজও ভুলতে পারিনি। মিলাদ শরিফ উপলক্ষ্যে স্কুলে মুসলমান ছেলেদের উৎসবেও সকলে মিলে যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করতাম। মুসলমান ছাত্ররা আমাদের মিষ্টি খাইয়ে আপ্যায়িত করত। আমরাও নিঃসংকোচে তা গ্রহণ করেছি, সবাই মিলে আনন্দ করেছি।
বৈশাখের ঝড়ে সে-এক রুদ্রমূর্তি চোখে পড়ত। শ্রাবণের বর্ষণে দিগন্তের কোণে কালো মেঘ নিরুদ্দেশ হয়ে যেত চলনবিলের ওপারে। আমাদের বাড়ির ঘরের টিনের চালে বিষ্টির আওয়াজ এক অদ্ভুত ঐকতানের সৃষ্টি করত। ধান লাগানোর জন্যে কৃষকের মন তখন চঞ্চল হয়ে উঠত। সময় সময় আমিও বাবার সঙ্গে ধান লাগানো দেখতে যেতাম। কাদার মধ্যে উপুড় হয়ে একসঙ্গে কৃষকদের ধান লাগানোর দৃশ্য অবর্ণনীয়। হেমন্তে যখন ধান উঠত কৃষকদের গোলায় তখন ভোরের দিকে পাশের পাড়া থেকে কৃষক-বউদের ধান ভানার আওয়াজ শুনতে পেতাম। সেই চেঁকির আওয়াজে কেমন জানি একটা গ্রামীণ আত্মীয়তার স্পর্শ লাগত মনে। মেয়েরা ধান ভানছে, কেউ-বা ধান ঢেলে দিচ্ছে গর্তে। আর নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে নানারকম গেরস্তির কথা। চমৎকার ঘরোয়া সেই রূপটি আজ কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছি। কখনো ধান ভানতে ভানতে মেয়েরা সুর করে গান ধরেছে। সে-গানের কলি আজ মনে নেই, কিন্তু সুরটা আজও বাজছে হৃদয়ের মাঝখানে।
বিকেলের দিকে আমরা কয়েকজন প্রায়ই কুঞ্জবাড়ির দিকে বেড়াতে যেতাম। নির্জন, নিস্তরঙ্গ সন্ধ্যা। রথের মেলা বসত এইখানটায়। দু-ধারে বন্য জামগাছের সারি। সামনে বিল। সূর্যাস্তের ছায়া পড়ে বিলের জল কেমন জানি অতীত-মুখর হয়ে উঠত। বহুদূর অতীতের কথা, রানি ভবানীর আমলের কথা, বাংলার বিগতশ্রী অবিস্মরণীয় দিনের কথা। কুঞ্জবাড়ির পথের বাঁ-দিকে একটা বটগাছের তলায় মুসলমানদের একটি পীঠস্থান আছে। গ্রামের হিন্দু মুসলমানদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে বছরে তিন দিন সেখানে গানের পালা হত। বিরাট চাঁদোয়া খাটানো হত ওপরে। সত্যপীরের গান, কৃষ্ণলীলার গান, দেহতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, মুক্তিতত্ত্ব সমস্ত কিছুই সেখানে গান গেয়ে আলোচনা করা হত। হিন্দু-মুসলিম সমস্ত গ্রামবাসী স্তব্ধ কৌতূহলী হয়ে সে-গান শুনত। গানের পালার মাঝে মাঝে ঢাক-ঢোল বেজে উঠত। পরচুলা ঝাঁকানি দিয়ে ঘন ঘন নৃত্য হত। অনেক হিন্দুও সেই দরগায় সিন্নি দিত, কেউ রুগণ ছেলের রোগমুক্তির জন্যে, কেউ হয়তো স্বামীর সুস্থতার জন্যে।
হাজরা নাটোর গ্রামের পাশ দিয়ে চলে গেছে জেলা বোর্ডের রাস্তা। দু-পাশে ঝাউগাছের সারি। তরুণদের মধ্যে সংগঠন গড়ে তোলবার জন্যে গ্রামে আমরা একটা পাঠাগার স্থাপন করেছিলাম। পাঠাগারের ভেতর দিয়ে গ্রামের তরুণদের রাজনীতিমূলক শিক্ষা দেওয়া হত। ভেবেছিলাম আমরা সমস্ত তরুণরা মিলে সংঘবদ্ধ হয়ে গ্রামের সেবা করব, সে-আশা আজ ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। এমনই ধূলিসাৎ হওয়া স্বপ্ন নিয়ে কলকাতার রাজপথে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল গ্রামের এক প্রতিবেশীর সঙ্গে। ‘হঠাৎ আপনি এখানে?’–বহুদিন পর দেখা হওয়ায় বিস্ময়ে প্রশ্ন করি। ‘এই এলুম একটু এদিকে, দেখি যদি কিছু সুবিধে হয়।– নিস্তেজ হতাশ উত্তর। কৃপাপ্রার্থীর ভাব তার কথায় আর হাবভাবে। দেশসেবার পুরস্কারস্বরূপ বহুকাল কারাজীবন অতিবাহিত করেছেন তিনি। কোনোদিন ভেঙে পড়েননি। আজ যেন সত্যিই তিনি ভেঙে পড়েছেন। একদিন এঁকে দেখেছি বিপুল প্রাণশক্তির প্রতীকরূপে। আজ কলকাতার জনারণ্যে তাঁর মধ্যে কোনো বিশেষত্ব খুঁজে পেলাম না। মিছিলের মধ্যে তিনিও মিশে গেছেন শরণার্থী হয়ে।
.
তালন্দ
উত্তরবঙ্গের রাজসাহী জেলার ছোট্ট এক টুকরো গ্রাম। তালন্দ তার নাম। পাশেই একদিকে ছড়ানো রয়েছে দীর্ঘ প্রসারিত বিল। অন্য দিকে ছোটো একটি জলরেখার মতো শীর্ণ শিব নদী। নদীটি ছোটো কিন্তু ঐতিহ্যে বিশিষ্ট। অনেক ইতিহাস-মুখর দিনের নীরব সাক্ষ্য বহন করছে এই নদী। আজ সে বিগতযৌবনা। বর্ষাকালে বিলের সঙ্গে মিশে নিজের অস্তিত্বটুকুও হারিয়ে ফেলে। পশ্চিম দিকে সজাগ প্রহরীর মতো ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চওড়া রাস্তাটা আরও উত্তরে বিলটিকে লাফিয়ে পার হয়ে দূরান্তের গ্রামের সঙ্গে মিশে গেছে।
গ্রামটি ছোটো। কিন্তু সুখ-সুবিধা অপ্রচুর নয়। রাজনৈতিক দূতক্রীড়ায় উলুখড়দের জীবনাবসান হয়েছে। কিন্তু তবুও ভুলতে পারি না ছেড়ে-আসা গ্রামের রাঙামাটির স্পর্শ। নুন তেল, রেশনকার্ড আর চাকরির বাইরে যখন মনের অবসর রেণু রেণু হয়ে উড়ে যায়, স্মৃতির টুকরো তখন ঘা দেয় অবচেতন মনের দরজায়।
প্রাণচঞ্চল গ্রাম্য আবহাওয়া প্রতিঋতুর সঙ্গেই পরিবর্তিত হয়ে যায়। গ্রীষ্মকালে কালবৈশাখীর সঙ্গে যখন আম কুড়োবার ধুম পড়ে, যখন আম-জাম-কাঁঠালের রসালো চেহারা লুব্ধ করে আমাদের, তখন গ্রামের বুকে দেখা দেয় ‘মাসনা’ খেলা। ঢাকের বাজনার সঙ্গে বিভিন্ন ঢঙের মুখোশ পরে নাচতে থাকে স্থানীয় খেলোয়াড়গণ এবং অনেক সময় চেতনা হারিয়ে ফেলে দর্শকদের রুদ্ধবাক চেহারার সামনে। গ্রীষ্মের শেষে আম-কাঁঠালের বিদায়কালে আকাশের চক্ষু যেন সজল হয়ে আসে–দেখা দেয় ‘শ্যামাঙ্গী বর্ষাসুন্দরী। বিলের দেহে আস্তে আস্তে জল জমতে থাকে। ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা ছোট্ট এক একটা হাত-ছিপ নিয়ে জল ঘুলিয়ে মাছ ধরে। দেখতে দেখতে তাদের ছোটো ছোটো খলই’ কই, রুই, সিঙ্গি, ট্যাংরা, পাবদা মাছে ভরে ওঠে। বিলের বুকে তখন দেখা যায় নৌকার কালো রেখা। দু-দিক থেকে নৌকাগুলো পরস্পরের কাছে এগিয়ে এসে পরমুহূর্তেই ছিটকে বেরিয়ে যায় বিপরীত দিকে। সেই সময় প্রশ্নোত্তর চলে—’লাও কোতদূর কারা? তানোরের’ ইত্যাদি। এরই সমসাময়িক আর এক অনুষ্ঠান শীতলা পুজো। ভক্তের ভক্তিনম্র ডাক পাষাণ-প্রতিমার প্রাণে সাড়া জাগায় কিনা জানি না, তবে এমন করেই কেটে যায় বর্ষার দুঃসহ পরিবেশ। মাটির বুকে জেগে ওঠে গুচ্ছ গুচ্ছ কাশফুল। হাতছানি দিয়ে তারা যেন ডাকে শরতের মেঘদলকে। টুকরো টুকরো মেঘও তাই মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে কাশফুলের শুভ্র অঙ্গে স্নেহের পরশ দেয়–নেমে আসে একপশলা বৃষ্টি। নির্মল আকাশের বুকে বকের ঝাঁক উড়ে চলে শরৎকে অভিনন্দন জানাতে। শুভ মুহূর্তে ধরণির বুকে নেমে আসেন দশপ্রহরণধারিণী মা। গ্রামের প্রান্তে প্রান্তে আনন্দের বন্যা ছুটে চলে। থিয়েটারে, নাচে, গানে, ঢাকের বাজনায় বছরের জমানো ক্লেদ যেন পরিষ্কার হয়ে যায়, মায়ের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। মায়ের বিদায়ে সান্ত্বনা দিতে হেমন্তে উঠে আসেন ধান্যলক্ষ্মী। নবান্নের উৎসবে আবার নতুন করে আলপনা পড়ে দুয়ারে দুয়ারে। মঙ্গলঘটের ওপর ধানের গুচ্ছ রেখে পুজো সারা হলে বাড়ি বাড়ি ঘুরে উৎসবের ভাগী হতে হয়। আস্তে আস্তে শীতের আমেজ পাওয়া যায়। পৌষ-সংক্রান্তিতে রাখালদের বাস্তু পুজো’র লোকসংগীত সারাদেশ ধ্বনিত করে। তার পরেও আছে পিঠেপুলি, চড়কপুজোর হইহই। এমনি করেই বছরের বারোটা মাস ঘুরে ঘুরে আসে ছোটো গ্রামখানির বুকের ওপর এবং তারা চিহ্নও রেখে যায় নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যের।
মনে পড়ে গ্রামের ডাকঘরটিকে। সারাদুনিয়ার পরিচয় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই ক্ষুদ্র ঘরটি। তার পাশেই দাঁতব্য চিকিৎসালয়, ছেলে-মেয়েদের হাই স্কুল, মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়। সংস্কৃত শিক্ষার্থীদের জন্যে টোল। তা ছাড়াও আছে পল্লি পাঠাগার ও ক্লাব। গ্রামটি স্বয়ংসম্পূর্ণ।
মাঝখানে একবার গিয়েছিলাম আমার ছেড়ে-আসা গ্রামের লাল মাটিতে। নজরে পড়ে গেল বাঁশবাগানের মাঝে পুরোনো মসজিদটার ওপর। দু-ধারের দুটি অশ্বত্থ গাছের চাপে অবস্থা তার বিপর্যস্ত। মনে হয় মুসলমানরাই এখানে প্রাচীন। পরে ক্রমশ হিন্দুপল্লি গড়ে উঠেছে এবং হিন্দুধর্মের নিদর্শন ছড়িয়ে পড়েছে এধারে-ওধারে। তালন্দের শিবমন্দিরের নাম ডাক আছে–তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি জনশ্রুতিতে,
বিল দেখিস তো ‘চলন’
আর শিব দেখিস তো ‘তালন’।।
গ্রামের মুসলমানরাও ছিল আমাদের আপনজন। পুজো-পার্বণে এদের অনেক সাহায্য পেয়েছি। গ্রামের কাজে এরা করেছে সহযোগিতা। কিন্তু আজ? একসুরে বাঁধা বীণার তার কোথায় যেন ছিঁড়ে গেছে। তাই আজ সুরহীন হয়ে পড়েছে সব। প্রাণমাতানো সংগীতের মীড়ে কোথায় যেন ঘটেছে ছন্দপতন। যে ক-দিন ছিলাম গ্রামে, গমকে গমকে এই কথাটাই প্রাণের ভেতর বেজেছে বেশি করে।
স্কুল দুটি প্রাণহীন, পাঠাগার অগোছালো, ক্লাবঘর স্তব্ধ; হাট, ঘাট ও মাঠে বিষাদের সুর। সারাগ্রামখানিই যেন ছেড়ে-যাওয়া একটা বাড়ি, স্থানে স্থানে পড়ে রয়েছে ছেঁড়া কাগজ, জিনিসপত্রের টুকরো–উঠে-যাওয়া বাসিন্দাদের অবস্থানের চিহ্ন।
শুধু একজনকে দেখলাম গ্রাম ছেড়ে চলে যাননি। তিনি হচ্ছেন গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ দাদু। মাটি-মায়ের প্রতি তাঁর ভালোবাসার তুলনা হয় না। প্রাণের মায়ায় মাটি ছেড়ে গিয়ে জন্মভূমিকে যারা ব্যথিত করেছে, তাদের দলে দাদু নন। তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন মানুষের শুভবুদ্ধির আশায়। তিনি যে দেশকে ভালোবাসেন।
তাঁর সম্বন্ধে অনেক টুকরো টুকরো ঘটনা মনে পড়ে। মনে পড়ে রাস্তা ছায়াচ্ছন্ন করবার জন্যে নিজের হাতে তাঁর গাছ লাগানোর কথা। যাতায়াতের সুবিধের জন্যে নিজের জমি কেটে রাস্তা করার কথা। গরিব কৃষকদের জন্যে কোঅপারেটিভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার কথা। জনসাধারণের প্রত্যেকটি ভালো কাজে দেখেছি তাঁর মঙ্গল হস্তের স্পর্শ। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাই।
রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে একবার ঠিক হয়েছিল, কিছু চাঁদা তুলে তাঁর স্মৃতিভান্ডারে পাঠানো হবে। দাদু শুনে বললেন—’টাকা পাঠাবে সে তত ভালো কথা। কিন্তু সেখানে টাকা পাঠাবার জন্যে অনেক বড়োলোক রয়েছেন। তোমাদের এই সামান্য টাকা সেখানে না পাঠিয়ে, তাই দিয়ে রবীন্দ্রনাথের বই কিনে সবাইকে পড়াও। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দাও। তবেই তো এরা বুঝবে রবীন্দ্রনাথ আমাদের কী ছিলেন।’ তাঁর কথা তখন কেউ শোনেননি। আত্মকেন্দ্রিক বলে সবাই তাঁর কথা উড়িয়ে দিয়েছিলেন। আজ কিন্তু তাঁর সে-কথার মর্মার্থ বেশ বুঝতে পারছি।
তিনি আধুনিক বাণীসর্বস্ব নেতাদের মতো বিশ্বপ্রেমিক না হতে পারেন, কিন্তু তাঁর দেশপ্রেম যে খাঁটি, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।
গ্রামের দেওয়ালে দেওয়ালে বর্ণপরিচয়ের প্রথম পাঠ তিনি লিখে দিয়েছিলেন জবাফুলের সাহায্যে। সংখ্যাতত্ত্বের পাঠও ছিল তার সঙ্গে। উদ্দেশ্য গণশিক্ষার প্রসার। গরিব কৃষকদের বই কিনে স্কুলে পড়া না হতে পারে, কিন্তু দেওয়ালের বড়ো বড়ো অক্ষরগুলো পড়ে অনায়াসেই তারা শিখতে পারবে মাতৃভাষা। পাঠাগারের গায়ে তিনি লিখে দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃমন্ত্র–বন্দেমাতরম। রাস্তার ওপরেই ছিল তাঁর বাড়ির চওড়া দেওয়াল। ওটাই হল দাদুর প্রচারকেন্দ্র। প্রায় দিনই দেখা যেত পঞ্চমুখী জবাফুল দিয়ে দাদু ওই দেওয়ালের গায়ে প্রাণ ঢালা ভাষায় লিখে চলেছেন গ্রামের খবর। সেই সঙ্গে থাকত কোথায় রাস্তা করতে হবে, গ্রামের কোন পুলটার মেরামত প্রয়োজন, কৃষকরা ঋণ পেয়ে কী করবে ইত্যাদি। এ ছাড়াও ছিল তাঁর চিঠিপত্র লেখা ও বৈঠকে ছোটো ছোটো বক্তৃতা দেবার বাতিক। এমনি করেই দেশসেবায় তিনি নিমগ্ন থাকতেন সবসময়, আর থাকবেনও জীবনের বাকি ক-টা দিন। দাদুর অর্থপ্রাচুর্য নেই, দল নেই, দলীয় প্রচারপত্রও নেই, কিন্তু যে-জিনিসের তিনি অধিকারী সে-জিনিসেরই আজ বড়ো বেশি অভাব। সে হচ্ছে তাঁর হৃদয়। বাংলার গ্রামের মানুষের সেই হৃদয় আজ হারিয়ে গেছে। সেই হৃদয়কে আবার উদ্ধার করতে হবে।
.
বীরকুৎসা
বীরকুৎসা কি কোনো গ্রামের নাম হতে পারে? যদিও-বা হয় তাহলে কী করে এ নাম হল সে-সম্পর্কে কোনো প্রশ্নের জবাব হয়তো দিতে পারতেন গ্রামের প্রাচীন প্রাজ্ঞরা। কিন্তু আমার তা জানা নেই। তবু আমার গ্রামের নাম বীরকুৎসা। রাজসাহী জেলার ছোট্ট একটি গ্রাম। আজ তার ইতিবৃত্ত বলতে বসে কেবলই মনে প্রশ্ন যাগে, সে গ্রাম কী করে এরই মধ্যে এত দূরের হয়ে গেল! ভাবতে কষ্ট হয়, তবু ভাবি। এখনও যেন স্পষ্ট দেখতে পাই ভোর হয়ে আসছে গ্রামের দিগন্তে। জেগে উঠেই দেখতাম তছির সর্দার আর শুকাই প্রামাণিক লাঙল কাঁধে নিয়ে সেই কুয়াশা-ছড়ানো নরম ভোরের আলো-আঁধারিতে গোরু নিয়ে চলেছে মাঠে। ওপাড়ার নলিন জেলে জনকয় সঙ্গী নিয়ে খুব বড়ো একটা বেড়াজাল কাঁধে ফেলে শীতে কাঁপতে কাঁপতে ছুটে চলেছে আত্রাই নদীর দিকে। এ সবই আজ আমার কাছে অতীত। অনেক দূরের ব্যাপার। তবু তো থেকে থেকে মন বলে, চলো সেখানেই যাই।
শহরে সময় চলে দৌড়ে, গ্রামে যেন তার কোনো তাড়াই নেই। ধীরেসুস্থে গড়িয়ে যায় প্রহরের পর প্রহর। ভোরের সূর্য ওঠে। পাশের গ্রাম দুর্লভপুরের উঁচু বটগাছটার মাথার ওপর দিয়ে সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ে বীরকুৎসার আনাচে-কানাচে। দেখতাম ওপাড়ার পূর্ণ সাহা কম্বল মুড়ি দিয়ে নিমের ডালে দাঁত ঘষতে ঘষতে আমাদের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াত। আর এ বছরের শীত যে খুব বেশি এবং গত আট-দশ বছরের মধ্যে তার কোনো তুলনা পাওয়া যায় কি না তারই ব্যর্থ আলোচনা নিয়ে সকালটা মাত করে রাখত। শহরে এসে যেদিকে তাকাই মানুষের হাতে গড়া ইট, কাঠ, পাথরের সৌধ। কিন্তু গ্রাম যেন মানুষের গড়া নয় প্রকৃতির দাক্ষিণ্যে সে যেন আপনাতে আপনিই বিকশিত। নরম মাটির গন্ধ, ভাঁটফুল, বনতুলসী আর ঘেঁটু ফুলের আরণ্যক সমৃদ্ধি মনকে এমনিতেই কেমন জানি উতলা করে রাখত।
বাড়ির দক্ষিণ দিকে ছিল ছোটো একটি খাল। বর্ষায় সেই বিশীর্ণ খালে আসত যৌবনের জোয়ার। উত্তরবঙ্গের মাঝিরা যে খাল বেয়ে যেত গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। নৌকার লগি ঠেলার আর বৈঠার টানের শব্দে কত রাত্রে ঘুম যেত ভেঙে। মনে হত গ্রাম মৃত্তিকার স্পন্দন-ধ্বনি শুনতে পাচ্ছি বুকের কাছটিতে।
গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ আশু দাদুর প্রকান্ড বৈঠকখানায় প্রতিসন্ধ্যায় বসত তরুণদের জলসা। সর্বজনীন কালীপুজো, দুর্গাপুজো প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষ্যে যাত্রা, থিয়েটারের গৌরচন্দ্রিকা অর্থাৎ মহড়া চলত সেখানে। পাঁচন মোল্লা, সরিতুল্লা, বৈদ্যনাথ আর ফকির পাল প্রভৃতি হিন্দু-মুসলমান মিলে যাত্রা গান প্রভৃতি অনুষ্ঠানে মেতে থাকত। সেদিন তো কোনো বিচ্ছেদ, বিভেদের প্রশ্ন ওঠেনি! বাহারদা ছিলেন বাঁশি বাজাতে ওস্তাদ। তাঁর বাঁশের বাঁশির সুরযোজনা গ্রামবাসীকে মুগ্ধ করেছে কত অলস অপরাহ্ন,ে কত সন্ধ্যায়। তিনি মুসলমান ছিলেন বলে তো হিন্দুর উৎসবে তাঁর আমন্ত্রণ বাদ পড়েনি আনন্দ পরিবেশনে? গ্রামের পোস্টমাস্টার ধীরেন মজুমদার ও পুরোহিত রুক্মিণী চক্রবর্তী ছিলেন রসিকপ্রবর। এঁদের মুখে সত্যি-মিথ্যে অতিরঞ্জিত কাহিনি শোনবার জন্যে গ্রামবাসীরা সাগ্রহে ভিড় করত। এঁদের সকলকে নিয়েই তো গ্রাম। তাঁদের ভুলি কী করে?
স্কুলের মাঠে খেলাধুলোর প্রায় সকলরকম ব্যবস্থাই ছিল। স্টেশনের অদূরে কুঁচেমারা’ নামে একটি রেলের সাঁকোর ওপরে ভিড় জমত ছেলে-বুড়ো অনেকেরই। এই আড্ডাটির লোভ সংবরণ করতে পারত না কেউ। শত কাজ ফেলেও সন্ধের দিকে কুঁচেমারা’ সাঁকোর কাছে যাওয়া চাই-ই। চমৎকার সে জায়গাটির পরিবেশ। একধারে সবুজ গ্রাম, আর একধারে বিস্তীর্ণ মাঠ। সূর্যাস্তের সময় কবিগুরুর কথা মনে হত– সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে। সাঁকোর তলা দিয়েই চলে গেছে খাল। সেখানে জেলেরা খেয়া পেতে মাছ ধরত। বড়ো বড়ো নৌকা পাল তুলে চলে যেত অনবরত। কোনো কোনো নৌকা জেলেনৌকার পাশে ভিড়িয়ে মাছ কিনে নিত।
গ্রামের জমিদার বাড়ির প্রাঙ্গণে অতীতকালের সাক্ষী রয়েছে এক বিরাট বকুলগাছ। চিরদন্ডায়মান গাছটি পথক্লান্ত পথিকদের যেন আহ্বান জানায়। গাছের তলাটি বহুদিন আগে জমিদার বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। বিরাট বাঁধানো বেদির ওপর কেউ কেউ তাস পাশা খেলায় মগ্ন থাকত, ছেলেরা ছক কেটে বকুলের বিচি সাজিয়ে ‘মোগল পাঠান’ প্রভৃতি খেলায় জমে যেত। ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েরা বকুল ফুলের মালা গাঁথবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ফুল কুড়োত।
নিকটেই ছিল ডাকঘর। ডাক-হরকরার প্রতীক্ষায় যুবক-বৃদ্ধ সবাই গাছটার তলায় জড়ো হত এবং ডাক পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গেই দু-তিনখানা পত্রিকা নিয়ে বকুলতলার আড্ডার প্রথমপর্ব শেষ করত। সংবাদপত্রের খবর নিয়ে মাঝে মাঝে বচসাও হত। এখন সেই বেদিটিতে বড়ো বড়ো ফাটল ধরেছে, সেখানে খবরের কাগজও আর পড়া হয় না, বকুলফুলও আর ছেলে-মেয়েদের আকর্ষণ করে না।
বৈশাখে একমাস ধরে ‘নগর-কীর্তন’–এপ্রথা বহুকালের। গ্রামের প্রান্তরে এক ঘন জঙ্গলে বুড়ো কালীর বাঁধানো বেদি এবং তারই পাশে প্রকান্ড এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। সেখান থেকে ‘নগর-কীর্তন’ আরম্ভ হয়ে নানা পথ ঘুরে আশু দাদুর মন্ডপে এসে শেষ হত। এতে কিশোরী চৌকিদার, জহিরউদ্দিন প্রভৃতি মুসলমানরাও যোগ দিত। এদের গাইবার ক্ষমতাও ছিল অসাধারণ। গ্রামে মহরমের মেলায় ‘তাজিয়া’ শোভাযাত্রায় রমেশ, টেপা প্রভৃতির লাঠি খেলা দর্শকদের অবাক করে দিত। তখন কেউ জানত না হিন্দু-মুসলমান দুটো পৃথক জাত। একটা মিথ্যেই শেষে সত্যি হল।
মাতব্বর হালিম চাচা সকালে কাশতে কাশতে বাজারে এসে গল্প জুড়ে দিতেন। তাঁর কথা বলার একটা অদ্ভুত ভঙ্গি ছিল। সব কথা সত্যি না হলেও কথার প্যাঁচে সবাইকে স্বমতে নিয়ে আসতেন। শান্তাহারের হাঙ্গামার পর যখন গ্রামকে গ্রাম হিন্দু-শূন্য হতে লাগল তখন তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন–বাবা কালা, মদা তুরা য্যাস না, আমরা গাঁয়ে থাকতে আল্লার মর্জিতে তুদের কিছু হবে না…। কিন্তু গ্রামের লোক সেদিন তাঁর কথায় আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারেনি। গ্রাম ছেড়ে আসার দিন আমার প্রিয় বন্ধু আহমেদ মিয়াও আমাকে বলেছিল–ভাই, তুইও আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছিস? এই কথাটির মধ্যে যে কত ব্যথা লুকোনো ছিল তা একমাত্র আমিই জানি। আজও মনে হয় হালিম চাচার, আহমেদ মিয়ার করুণ স্নেহ-সম্ভাষণ। আমাদের মাঝখানের এই দুস্তর ব্যবধান একদিন ঘুচবেই। মিথ্যে তো কখনো সত্যি হতে পারে না!
শ্রীহট্ট – পঞ্চখন্ড রামচন্দ্রপুর
পঞ্চখন্ড
বাংলার পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত শ্রীভূমি। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের পদধূলি লাঞ্ছিত, অদ্বৈতাচার্য ও দেশনায়ক বিপিন পালের জন্মস্থান পবিত্র শ্রীভূমি। তারই কোলে সদা উজ্জ্বল আমার গ্রাম পঞ্চখন্ড। বাংলার হাজার গ্রামের মধ্যে আমার গ্রাম অনন্যা। অদূরে উত্তাল প্রবহমান নদ ব্রহ্মপুত্র, তার শাখানদী কুশিয়ারা। বৈষ্ণবতীর্থ পঞ্চখন্ড, পার্শ্ববর্তী গ্রাম ঢাকা-দক্ষিণ। অতীতে বাংলা ও বাংলার বাইরে থেকে সমাগত বিদ্যার্থী পুণ্যার্থীদের চরণস্পর্শে ধন্য হয়ে যেত এই গ্রাম। যাঁরা আসতেন, তাঁরাও এ গ্রামের সান্নিধ্যে এসে নতুন প্রেরণা অঞ্জলি ভরে গ্রহণ করে নিয়ে যেতেন। মহাপ্রভূর বৈষ্ণবধর্মের দীক্ষায়, জ্ঞানে-গরিমায় পুণ্যব্রতা এই গ্রাম।
তার কথা বলতে গিয়ে মন চলে যায় অতীতে, অনেক দূরের অতীতে। মনের অলিতে গলিতে এলোমেলো ভাবনার ভিড়। তন্ময়তায় একেবারে ডুবে যাই। হঠাৎ যেন একটানা বাঁশির শব্দে চমকে উঠি। ওপার থেকে যাত্রী নিয়ে স্টিমার ছাড়ল। আমিনগাঁও রেল কোম্পানির বিজলি বাতি ঝিকমিক করছে এপার থেকে। নদ ব্রহ্মপুত্র। নিস্তরঙ্গ জলরাশি। একখানি শূন্য নৌকা ধীরে ধীরে ভিড়ছে পারে। কয়েক বছর আগে কুশিয়ারার তীরে বসে শেষদেখা সেই খেয়া নৌকা পারাপারের দৃশ্য মনে পড়ে গেল। কোনো মাঝি উদাস সুরে গান ধরেছে : ওরে বধূর লাইগ্যা পরান কান্দে মোর। সে গান আর শোনবার সৌভাগ্য হয় না। মনে পড়ছে গ্রামের সুধীনদাকে। গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় হৃষ্টপুষ্ট মানুষটি। সবসময় মুখে হাসি লেগেই রয়েছে। আমাদের শৈশবকালে তিনি ছিলেন এক পরম বিস্ময়। এই লোকটিকে ধরতে কত পুলিশ-দারোগাকে কতবার নাজেহাল হতে হয়েছে। কত দিন মুগ্ধ বিস্ময়ে সে যুগের কীর্তি-কাহিনি শুনেছি তাঁর মুখে। রূপকথার মতো মনে হয়। বনজঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ক্লান্তি ধরে গেছে। পেছনে ঘুরছে প্রেতের মতো বিদেশি আমলের আই-বি-র দল। বোমা তৈরি আর পিস্তল চালাবার ট্রেনিং দেওয়া হয় শিয়ালকুচির জঙ্গলে। সে-যুগও চলে যায়। আসে অসহযোগ আন্দোলনের দিন। মাঠের মাঝখানে সার দিয়ে দেশকর্মীদের দাঁড় করায় অত্যাচারী দারোগা কেশব রায়। পিঠ ফুটে রক্ত বেরোয়। চোখ অন্ধকার হয়ে আসে। তবুও প্রাণপণে অস্ফুটস্বরে প্রতিকণ্ঠে উচ্চারিত হয় ‘বন্দেমাতরম’ মন্ত্র।
সুধীনদা আশা দিয়ে বলতেন : আর দুঃখ কী? স্বাধীনতা এল বলে। ভাবী দিনের ভাবী মানুষ তোরা, দুঃখজয়ী কিশোর তরুণের দল।… আর কথা শেষ করতে পারেন না। দু-হাত দিয়ে বুক চেপে ধরেন। অনেকদিন ধরে এই এক যন্ত্রণায় ভুগছেন সুধীনদা। সেই যে-বার পুলিশ সুপারের সঙ্গিনের আঘাতে বুকের একটি পাঁজর ভেঙে গিয়েছিল, তখন থেকেই একটানা কথা বলতে কষ্ট হত সুধীনদার। আজ কোথায় তিনি। হয়তো স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে কোনো এক উদবাস্তু শিবিরে আশ্রয় নিয়ে তিনি প্রাণ-রক্ষার দুস্তর প্রয়াস করছেন।
গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে আমরা গড়ে তুলেছিলাম কিশোর লাইব্রেরি। করোগেটেড টিনের ছাউনি দেওয়া ছোটো ঘর। কিশোরদের জন্যে হলেও সেটা ছিল গ্রামের সকলের প্রাণ। যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলের অবসর বিনোদনের একমাত্র আশ্রয়কেন্দ্র। লাইব্রেরির পাশেই খেলার মাঠ। ফুটবল খেলার মরশুমে একটা-না-একটা প্রতিযোগিতা লেগেই থাকত প্রতিদিন। অগণিত দর্শক। শুধু ছেলেরাই নয়–হুঁকো হাতে নিয়ে প্রৌঢ়-বৃদ্ধরাও মাঠের সামনে এসে জড়ো হতেন।
বর্ষাকালে খালে-বিলে মাঠে ধু-ধু করছে জল–সমুদ্রের বুকে যেন গ্রামটি নির্জন একটি দ্বীপ। শুরু হয় নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা। প্রতিপক্ষের চিৎকার–নৌকার দাঁড়ের শব্দ আর অসংখ্য দর্শকের উজ্জ্বল কলরব–কী ঊর্মিমুখর জীবন! মনে পড়ে ছোটো গ্রামখানার ছোটো ছোটো মানুষগুলোকে। বহির্জগতের সঙ্গে হয়তো তাদের সম্পর্ক ছিল না–নিজের গ্রাম এবং আশপাশে আত্মীয়স্বজন ছাড়া বহু মানুষের সঙ্গে হয়তো তারা মেশেনি,তবু কত সরল তাদের অন্তর কত বিষয়ে কত বাস্তব অভিজ্ঞতা! আকাশের দিকে চেয়ে ঠিক বলতে পারবে তারা, বৃষ্টি কখন হবে। সবুজ মাঠটার দিকে একবার স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি বুলিয়েই আনন্দে হয়তো মুখমন্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল একজনের। সে বললে-ফসল এবার হবে ভালো। আর ডোবার জল দেখে নির্ঘাৎ বলে দিল–প্রচুর মাছ আছে এর ভেতর। আশ্চর্য মানুষ এরা, বিচিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতালব্ধ এদের জীবন। নবীন মাঝি, তারক দাস, করিমুদ্দিন, শেখ সমীর এদের কি কখনো ভোলা যায়? প্রতিবার বাড়ি গেলে ঠিক এসে একবারটি খবর নেবে সমীর –ক্যামন আছ। তারপর এক কাঁদিকলা, নিজ হাতে ফলানো শাকসবজি নিয়ে এসে বাড়ি উপস্থিত–দাদাবাবুর লাইগ্যা আনলাম। পাষাণ-হৃদয় ছিল করিমুদ্দিন। একে একে তিনটি ছেলে এবং বউ একই মাসের ভেতর কলেরায় মরবার পরও লোকটাকে বিচলিত হতে দেখেনি কেউ। কিন্তু আমি জানি সেটা যে কত মিথ্যা। তার ভেতরের রূপ যে বাইরের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। …একা রাস্তা দিয়ে চলতে চলতে গ্রাম ছাড়িয়ে কবরখানার কাছে পৌঁছেছি। সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকার মিলিয়ে গেছে। সমস্ত শরীর ভয়ে শিউরে উঠল। ওই যে অল্প দূরে কী যেন নড়ছে, কে ও? স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু একী, মূর্তিটা যে ক্রমশ এগিয়ে আসছে। তবে যাই হোক, এ প্রেত নয়। কাছে আসতে বিস্ময়ের সীমা রইল না। আমায় সামনে দেখে হাউ হাউ করে কান্না শুরু করল করিমুদ্দিন। হঠাৎ খেয়াল হল। বহুদিনের নিরুদ্ধ আবেগ আর বাঁধ মানছে না করিমুদ্দিনের। মাথায় হাত দিয়ে রাস্তার ওপরেই বসে পড়ল আকাশের দিকে হাঁ করে চেয়ে। সান্ত্বনা দেবার মতো আমার কিছুই ছিল না, ধীরে ধীরে হাত দুটো ধরে অনেক দূর অবধি আনলাম ওকে। ওর মনের ভাষাটা তখন ঠিক রূপ নিয়েছে। যেন-’মোর জীবনের রোজ কেয়ামত, ভাবিতেছি, কতদূর!
সেদিন আর আজ। দুস্তর সমুদ্রের ব্যবধান। রাজনৈতিক পঙ্কিলতায় ডুবে আজ মানুষের মন বিষাক্ত, হিংস্রতায় পরিপূর্ণ। কিন্তু চিরকালই কি এমন ছিল? হিন্দুর বহু ধর্মীয় উৎসবে যোগদান করেছে মুসলমান। আমাদের বারোয়ারি কালীপুজোয় যে শখের যাত্রা হত, তাতে বহু মুসলমানকে দেখেছি ছড়ি হাতে নিয়ে অশান্ত জনতাকে শান্ত করতে। আর প্রতিবছর মহরমের দিন গাজনতলায় যে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হত, তাতে নিজ গ্রামের খেলোয়াড়দের অপূর্ব ক্রীড়ানৈপুণ্যে আমার বুকও কি গর্বে দশ হাত উঁচু হয়ে উঠেনি! সেসব তো আজ অতীতের বিস্মৃতপ্রায় স্বল্পকাহিনি!
আগে গ্রামে বিদ্যাচর্চার খুবই সুযোগসুবিধা ছিল। তর্করত্নমশাইদের চতুষ্পঠীতে বহুদূরদেশ থেকে লোক বিদ্যার্জন করতে আসত। আজ আর তার চিহ্ন নেই। ছিল ভাঙা আটচালায় গুটিকয় ছাত্র নিয়ে অপুর পাঠশালা। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। সবই পরিবর্তিত হয়ে গেছে। শুধু বাইরে নয়, অন্তরেও চিড় ধরেছিল বহুদিন থেকেই। শ্রীহট্টে গণভোটের সময় চিরশান্ত রসিদ, যাকে শ্রদ্ধা করতাম, গ্রাম্য সম্পর্কে চাচা বলে সম্বোধন করতাম তার কথাবার্তায় পর্যন্ত উন্মা ও অবর্ণনীয় ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছে দেখে বিস্মিত হয়েছি, দুঃখ পেয়েছি। মর্মান্তিক দুঃখে বিষণ্ণ বোধ করেছি রানিদির কথা ভেবে। লক্ষ্মীর প্রতিমার মতো রূপ। স্নেহমধুর ব্যবহার। বিয়ের কিছুদিন পরই বিধবা হয়ে অবাঞ্ছিতরূপে ফিরে এসেছিলেন বাপ-ভাইয়ের সংসারে। তবু আমাদের জন্যে তাঁর স্নেহধারায় কার্পণ্য হয়নি কোনোদিন। আজ শ্রীকান্তের মতোই বলতে ইচ্ছে করে, বাংলার পথে-ঘাটে মা-বোন। সাধ্য কি এঁদের স্নেহ এড়িয়ে যাই। সেদিন কলকাতার মেসে এক রুদ্ধ কোঠায় আঝোরে অশ্রুপাত করে ডেকেছি রানিদিকে।
গ্রামের কথা বলতে বলতে গ্রামের যত সব সোনার মানুষেরই ভিড় জমে ওঠে মনে। যদি এতে ইতিহাস না থাকে, চিত্র না থাকে, আমি নিরুপায়। আমার কাছে এদের প্রত্যেকেই অপরিহার্যরূপে আজও চিরঅমলিন। আমার পঞ্চখন্ডকে আমি ফিরে পেতে চাই, ফিরে পেতে চাই আমার আপনজনকে। হয়তো পাব। ইতিহাস তো আগে থেকে কোনো কথা বলে না।
.
রামচন্দ্রপুর
‘স্বদেশ স্বদেশ করিস কেন, এদেশ তোদের নয়’–চারণ-কবির এই গান আমরা সমবেত কণ্ঠে গেয়েছি ছোটোবেলায় আমাদের সোনার গ্রামের পথে পথে। গ্রামের মেয়ে-বধূ আর শিশু-বৃদ্ধের দল সার বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছে পথের দু-ধারে, স্বেচ্ছাসেবক দলের গানে তারাও অভিভূত হয়েছে। এক এক সময় তাদের চোখে দেখেছি জল, মুখময় যেন কী বেদনা! পরদেশি শাসনের তীব্র জ্বালা। কিন্তু আজ! ব্রিটিশ শাসনমুক্ত দেশের মাটিতেও আজ আমার অধিকার নেই! পিতৃপুরুষের যে ভিটেকে মায়ের মতো ভালোবেসেছি, যে মাটিকে প্রণাম করে বিদেশি শাসকের রোষবহ্নিকে বরণ করে নিয়েছিলাম, স্বপ্নময় কৈশোরে আমার জন্মভূমি জননীকে একদিন নবারুণালোকে স্বাধীনতার স্বর্ণ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখব আশায়, সেই মাটিই যেন আজ বিরূপ! স্নেহময়ী সেই মাটির মায়ের কোথায় সেই অভয়া রূপ? তার কোল-ছাড়া ভিটে-ছাড়া হয়ে আজ ছিন্ন-ভিন্ন আমরা। কোথায় মায়ের অভয় আহ্বান? কবির গানই কি তবে সত্যি–স্বদেশ মোদের নয়, দেশের মাটিতে নেই আমাদের কোনো অধিকার? মাতৃপূজার এই কি পুরস্কার?
মনে পড়ে স্বদেশি যুগের কথা। কবিগুরুর রাখিবন্ধনের গান গেয়েই আমরা ক্ষান্ত হইনি, মনেপ্রাণে রূপায়িত করেছি কবির বাণী ও প্রেরণাকে। কে হিন্দু, কে মুসলমান এ প্রশ্ন বড়ো করে কোনোদিনই আমাদের মনে আসেনি। ভাই ভাই হয়েই আমরা কাজ করেছি পল্লি উন্নয়নে, দেশ ও দেশবাসীর সেবায়।
আমার প্রতিবেশী মুসলমান বন্ধু যেদিন গাঁয়ের মাটি ছেড়ে দূরপথের যাত্রী হল অর্থান্বেষণে সে-দিন তাকে বিদায় দিতে যে বেদনা বোধ করেছিলাম সে তো আত্মীয়-বিরহেরই ব্যথা। সেই দূরবাসী বন্ধুর পথের আশায় ডাকঘরে যেয়ে যেয়ে আমার কৈশোর-জীবনের কতদিন যে হতাশায় ভরে উঠেছে আজও মনে জাগে তার বেদনাময় স্মৃতি, আবার এক একদিন তার পত্র হাতে নিয়ে যে কত উৎফুল্ল হয়ে বাড়ি ফিরেছি সে-কথাও ভুলে যাইনি। কিন্তু কোথায় আজ সেই বন্ধু? আজ আমি যখন ছন্নছাড়া শরণার্থীর বেশে কলকাতার জনারণ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি, আমার সেই প্রাণের বন্ধু আমার কথা কি মুহূর্তের জন্যেও ভাবছে? সাতপুরুষের ভিটেমাটি পুণ্য জন্মভূমি ছেড়ে আমরা যেদিন মান-প্রাণের দায়ে বেরিয়ে পড়লাম নিরুদ্দেশ যাত্রায় সে-দিন তো বন্ধু এসে বাধা দিল না বা আর কোনো মুসলমান প্রতিবেশী এসে বারণ করল না চলে আসতে গ্রাম ছেড়ে!
টম যেন বুঝতে পেরেছিল দু-দিন আগেই যে, আমরা চলে যাচ্ছি কোথায় কোন অজানা দেশে। আসার আগের দিন সারারাত ধরে টমের সে কী কান্না! রওনা হবার দিন সকালবেলাও খোকন মুঠো মুঠো ভাত দিয়েছে টমকে, কিন্তু টম শুধু তার ল্যাজ নেড়ে খোকনের গা ঘেঁষে এসে কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে ভাতে আর মুখ দেয়নি।
মিনি বেড়ালটাও পিছু নিয়েছিল ক-দিন ধরে। বাড়ির ছেলে-মেয়েগুলোর কতই না প্রিয় সে। শেষ দু-দিন দেখেছি আমাকেই আটকে দেবার জন্যে সে যেন একটা প্ল্যান করেছিল। তা na হলে কোনোদিন সে যা করেনি তা করবে কেন? চলে আসার আগের পরপর দু-রাত মিনি আমার বিছানায় ঠিক আমার পায়ের তলায় শুয়ে কাটিয়েছে। ঘুমের আবেশে তার মিনতিভরা স্পর্শও যেন অনুভব করেছি। সকাল বেলা জেগে উঠে লক্ষ করেছি তার সকরুণ বিমর্ষতা!
খোকন একবার বলেছিল, টম আর মিনিকে সঙ্গে করে নিয়ে চলো না বাবা! খোকনের মাও সায় দিয়েছিলেন তাতে। আমার মনে প্রশ্ন জাগল; ওরা কী দোষ করেছে? ওদের কেন অকারণে দেশছাড়া ভিটেছাড়া করব? রাজনীতির পঙ্কিলতায় ওরা তো মাথা গলায়নি!
কিন্তু তাতে কী? মানুষেরই প্রতিপালিত জীব ওরা, মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত ওদেরও কিছুটা করতেই হবে। তাই আমাদেরই পাপে দেশবিভাগের সম্মতির পরিণামে পরিজনহীন কত টম কত মিনি যে বেদনা-বিহ্বল হয়ে দিন কাটাচ্ছে আজ, কে তার হিসেব রাখে?
আচ্ছা, আমাদের টম, আমাদের মিনি এখনও কি আমাদেরই বাড়িতে আছে? টম কি আজও শুয়ে থাকে টেকিঘরের বারান্দায় তারই গড়া গর্তটার মধ্যে? অপরিচিতের পদশব্দে আজও কি টম তেমনই গর্জে ওঠে প্রহরীর কর্তব্য পালন করতে? ইঁদুর, পোকামাকড় এমনকী সাপ দেখেও মিনি কি এখনও তেমনই তেড়ে যায়? ওরা হয়তো আজও খুঁজে বেড়ায় খোকনকে এঘরে-ওঘরে, বাড়ির উঠোনের পেছনে, আর তার সঙ্গ না পেয়ে, আমাদের কাউকে না দেখে হয়তো ডুকরে কাঁদে!
আর আমাদের মুসলমান প্রতিবেশীরা? যুগ যুগ ধরে পারস্পরিক সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে যাদের সঙ্গে পাশাপাশি বাস করেছি, তারা একটুও কি দুঃখবোধ করল না আমাদের ছেড়ে দিতে? ওরা দাদা ডেকেছে, মামা ডেকেছে, আমরাও ওদের কাউকে ডেকেছি চাচা, আবার কাউকে ডেকেছি নানা। রাজনীতির খাঁড়ার কোপে যুগ-যুগান্তের সেই আত্মীয়দের সম্পর্কে কি চিরতরে ছেদ পড়ে গেল? ওদের কারও কারও মনের মণিকোঠায় হয়তো আজও আমাদের কথা জাগে। কিন্তু ওদের সঙ্গে প্রতিবেশীরূপে আর কি কোনোদিন দেখা হবে না?
গ্রাম ছেড়ে আসার দিনই অসময়ে একটা কাক ডেকে গিয়েছিল আমাদের বাড়ির ওপর দিয়ে। সে-ডাকে শুনেছিলাম কান্নার সুর। কাকের কণ্ঠ মনে রাখার মতো নয়। তবু কেন পল্লিমায়ের কোল-ছাড়া হয়ে আসার একটু আগে শোনা শেষ কাক-স্বর আজও কানে বাজে!
নিতান্ত গন্ডগ্রাম হলেও শ্রীভূমি শ্রীহট্টে একটা গৌরবময় স্থান অধিকার করে রয়েছে আমার সাধের গ্রাম রামচন্দ্রপুর আর তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। ক্ষুদ্র নবদ্বীপ বলে পরিচিত যে পঞ্চখন্ড, সংস্কৃত শিক্ষার অন্যতম সেই কেন্দ্রভূমিরই একাংশ আমাদের গ্রাম। মোট আট-দশ হাজার অধিবাসীর মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয় ভারতীয় শিক্ষিতের গড়পড়তা হারের তুলনায়। তাঁরা প্রত্যেকেই গর্ব করে এসেছেন এতকাল এই বলে যে, এমন এক ঐতিহাসিক গ্রামে তাঁদের বাস যার অন্তত হাজার বছরের প্রাচীনত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে তাঁদের সামনে।
কুমার ভাস্কর বর্মার তাম্রশাসনের কথা বলছি। কামরূপের রাজা ছিলেন কুমার ভাস্কর বর্মা। থানেশ্বরের অধীশ্বর দানশীল হর্ষবর্ধন শিলাদিত্যের তিনি ছিলেন সমসাময়িক। আমাদের গ্রাম থেকে মাত্র দু-মাইল দূরে আবিষ্কৃত হয়েছে ভাস্কর বর্মার তাম্রশাসন। সেই তাম্রশাসনে বর্ণিত কুশারী নদী আজও বয়ে চলে আমাদেরই গ্রামের পাশ দিয়ে। গাঙ্গুলি ও চন্দ্রগ্রামের ইতিকথা কিছু না জানা থাকলেও তাম্রশাসনের উল্লেখ থেকে আমাদের অঞ্চলবর্তী এ দুটি গ্রামের প্রাচীনত্ব ধারণা করা যেতে পারে।
শুধু কি এই? কত স্মরণীয় কত বরণীয়ের আবির্ভাব ঘটেছে আমাদের এ অঞ্চলে। পাশের গ্রাম দিঘিরপারে জন্মেছিলেন সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি। ছেলেবেলায় পড়েছি রঘুনাথের ছোটোবেলার কথা। কী অপরিসীম বুদ্ধি ছিল তাঁর অতটুকু বয়সে! পরবর্তীকালে যাঁর প্রতিভার দীপ্তি সারাভারতকে প্রদীপ্ত করেছিল, তিনি ছিলেন আমারই পূর্বপুরুষের প্রতিবেশী, বন্ধুজন হয়তো–একথা ভাবতেও শিহরন অনুভব করি। সেকালে ছিল না বৈদ্যুতিক আলো, ছিল না দেশলাই। আগুন ধরানো হত চকমকির সাহায্যে। তাও গরিবের পক্ষে ছিল দুর্লভ। পাঁচ বছরের শিশু রঘুনাথকে তাঁর মা বলেছিলেন একটু আগুন নিয়ে আসতে উনুন ধরাবার জন্যে। রঘুনাথ পাশের বাড়ির গিন্নির কাছে গিয়ে চাইলেন একটু আগুন। গিন্নি জিজ্ঞেস করলেন আগুন নেবার পাত্র কোথায়? রঘুনাথ তখন এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে পেলেন রান্নাঘরের পাশেই এক ছাইয়ের স্তূপ। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দু-হাত ভরে ছাই তুলে নিয়ে আবার গেলেন প্রতিবেশী গিন্নিমায়ের কাছে। গিন্নিমা বিস্মিত হয়ে একবার চাইলেন তাঁর দিকে, তারপর একহাতা আগুন তুলে দিলেন হাতের ওপরকার সেই ছাইয়ের ওপর। রঘুনাথ হাসতে হাসতে এগিয়ে চললেন তাঁদের বাড়ির দিকে। সম্মুখেই টোল। পন্ডিতমশাইয়ের চোখে পড়ল এই বিস্ময়কর ব্যাপার? রঘুনাথকে ডেকে তিনি জিজ্ঞেস করে শুনলেন সব কথা। সব দেখেশুনে তাঁর মায়েরও বিস্ময়ের অবধি রইল না। নিতান্ত দরিদ্র পরিবারের ছেলে রঘুনাথ। ছেলেকে টোলে পড়াবার সাধ থাকলেও বাপ-মায়ের সে সাধ্য ছিল না। কিন্তু সেদিনকার সে-ঘটনায় বিমোহিত পন্ডিতমশাই রঘুনাথকে নিজে ডেকে নিয়ে বিনে পয়সায় তাঁর টোলে পড়াতে লাগলেন। সেই কবে পড়েছি এই গল্প, আজও ভুলিনি। ভোলা যে যায় না।
শ্রীচৈতন্যের জন্মপূত ঢাকা-দক্ষিণ সারাভারতের তীর্থক্ষেত্র। মাত্র সাত মাইলের পথ সে গ্রাম আমাদের বাড়ি থেকে। শ্ৰীমনমহাপ্রভুর বাড়িতে যথারীতি পূজার্চনা চলছে শুনে এসেছি। নিত্য কীর্তনের ব্যবস্থাও নাকি এখনও অব্যাহত আছে। চৈতন্যদেবের জ্ঞাতি বংশের লোকেরা আজও সেখানে রয়েছেন। কতদিন থাকতে পারবেন তাঁরা জানি না। তবে প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গের সংকীর্তনে নবদ্বীপের পথে পথে একদিন যেমন ভক্তিরসে মেতে উঠেছিল হিন্দু মুসলমান একযোগে, ক্ষুদ্র নবদ্বীপ’ পঞ্চখন্ডে তেমন দিন দেখা দেবে সে-আশা নিতান্তই দুরাশা। এ যুগে যবন হরিদাসের আবির্ভাব একান্তই যেন অসম্ভব, ব্রাহ্মণ কালাপাহাড়েরই ছড়াছড়ি চারদিকে। তাই তো দেশেমাতৃকার দেহ-খন্ডন, তাই তো আজকের এই সর্বনাশ এই হাহাকার।
অমাবস্যার আকাশে পূর্ণচন্দ্র! এও কি সম্ভব? সম্ভব নাকি হয়েছিল এরূপ জনশ্রুতি রয়েছে। অমাবস্যায় পূর্ণিমার চাঁদ দেখেছিলেন আমাদেরই প্রতিবেশী ত্রিপুরা জেলার মেহের কালীবাড়ির সুপ্রসিদ্ধ সাধক সর্বানন্দ ঠাকুর আর আমাদের গুরুবংশের আদিপুরুষ ‘ত্রিশূলী’মশাই। ত্রিশূলী-র কালী’ আজও নাকি পুজো পান আমার গাঁয়ের মানুষের কাছে। কিন্তু পাপশক্তির বিনাশে মায়ের খঙ্গ তো আর নেচে ওঠে না! ‘ত্রিশূলী’-র বংশধরেরা তাই বুঝি আজ ত্রিপুরা রাজ্যে পলাতক!
ছোট্ট গ্রাম রামচন্দ্রপুরের অধিকাংশ জমির মালিকই ছোটো ছোটো জমিদার আর তালুকদার। তাঁদের মধ্যে হিন্দুও আছেন, মুসলমানও আছেন। গ্রামের মধ্যে বিশেষ করে তাঁরাই সম্পন্ন, তাঁরাই শিক্ষিত এবং তাঁদেরই অর্থে ও চেষ্টায় গড়ে উঠেছে পল্লির ছেলে মেয়েদের বিদ্যায়তন, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ডাকঘর, ক্লাব ইত্যাদি। তবে শিক্ষাদীক্ষায় স্থানীয়
হিন্দুরাই বেশি উন্নত এবং এগ্রামের প্রতিষ্ঠাতাও কায়স্থ ভূস্বামীরাই। আর সব জায়গার মতো আমাদের গ্রামেও ঝগড়াবিবাদ ছিল। লড়াই ও লাঠালাঠির কথা শুনেছি, দেখেছিও। কিন্তু সেসবই ছিল জমিদারির লড়াই। সেসব লড়াই আর লাঠালাঠি তালুকদারে তালুকদারে হয়েছে–হিন্দু-মুসলমানের কথা তাতে কোনোদিন ওঠেনি। হয়তো কোনো ধান খেতে একটা আল নিয়ে ঝগড়া বেধেছে একজন হিন্দু আর একজন মুসলমান তালুকদারের মধ্যে। দেখা গেল বাকি কয়জন মুসলমান তালুকদারই যোগ দিয়েছেন হিন্দু তালুকদারের পক্ষে, আবার কয়েকজন হিন্দু ভূস্বামী সাহায্য করছেন তাঁদের বিবাদমান মুসলমান প্রতিবেশীকে। এমন ঘটনা অনেকবারই নাকি ঘটেছে আমাদের গাঁয়ে এবং পাশাপাশি এলাকায়।
সাধারণ হিন্দু-মুসলমান একে অন্যকে সাহায্য করেছেন, পাকিস্তান সৃষ্টির বছরেও এমন ঘটনা খুঁজে বেড়াতে হত না। কিছুকাল আগের কথা। সম্ভ্রান্ত তালুকদার উজির আলি ভাগ্য বিপর্যয়ে অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েছেন। বাবার চেয়ে বয়েসে কিছু ছোটো হলেও একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাঁদের মধ্যে। উজির আলি সাহেবকে ডেকে পাঠালেন বাবা। তিনি এলেন এবং বন্ধুর মতোই বাবা তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, ‘উজির, শুনছি পারিবারিক মর্যাদা বজায় রেখে সংসার চালানোই নাকি তোমার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছে। তার জন্যে চিন্তা কোরো না ভাই।’ এই বলে বাবা বিনে খাজনায় ভোগস্বত্ব দিয়ে বারো বিঘের একটা ধানজমি লিখে দিলেন উজির আলি সাহেবকে।
স্বাধীনতার সংগ্রামী হিসেবে বিদেশি শাসক আর তার পদলেহীদের হাতে লাঞ্ছনা সয়েছি দীর্ঘকাল ধরে; কিন্তু মনে আনন্দের ভাটা পড়েনি তাতে কোনোদিন। বরং ওদের বাঁধান যতই শক্ত হবে, ততই বাঁধন ঠুটবে মোদের ততই বাঁধন টুটবে।”- মহাজনের এই মহাবাণী লক্ষ্যসাধনে আমাদের মনোবলকে চতুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। শত নির্যাতনের মধ্যেও দেশবাসীর অপার স্নেহ ও প্রীতি আমাদের কৃতজ্ঞতায় ভারাক্রান্ত। সেই দেশবাসীর একাংশ বিষের বাঁশি বাজিয়ে আমাদের করল ঘরছাড়া।