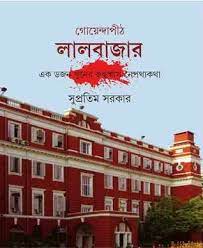- বইয়ের নামঃ গোয়েন্দাপীঠ লালবাজার
- লেখকের নামঃ সুপ্রতিম সরকার
- প্রকাশনাঃ আনন্দ পাবলিশার্স (ভারত)
- বিভাগসমূহঃ গোয়েন্দা কাহিনী
১. গোয়েন্দাপীঠ লালবাজার – ১ম খণ্ড
ভূমিকা
এই বইয়ের ভূমিকা লেখার অনুরোধটি যখন এল, অস্বীকার করব না, একটু চিন্তিতই হয়ে পড়েছিলাম।
বইটিতে সংকলিত সুপ্রতিম সরকারের লেখাগুলি সাইবার-দুনিয়ায় উচ্চপ্রশংসিত হয়েছে। সাম্প্রতিক অতীতে বাংলায় এমন মনোগ্রাহী রহস্যকাহিনি লেখা হয়নি, মত পোষণ করেছেন বহু পাঠক-পাঠিকা। বইয়ের আকারে যখন প্রকাশিত হচ্ছে সেই লেখাগুলি, কীভাবে শুরু করব মুখবন্ধ, ধন্দে ছিলাম তা নিয়ে। ইন্টারনেটের শরণাপন্ন হয়ে অস্বস্তি আরও বাড়ল, যখন দেখলাম বইয়ের ভূমিকা তাঁদেরই সচরাচর লিখতে বলা হয়, যাঁদের নিজেদের প্রকাশিত বই রয়েছে, বা যাঁরা বিরল কোনও কৃতিত্বের অধিকারী। আমার ক্ষেত্রে উপরোক্ত দুটি শর্তের কোনওটিই প্রযোজ্য নয়। ব্যক্তিপরিচয়ে নয়, ভারতের অন্যতম দক্ষ পুলিশবাহিনীর প্রধান হিসেবেই এই ভূমিকা লেখা।
একটু তলিয়ে ভেবে অবশ্য মনে হল, ভাল লেখকদের যা যা বই পড়েছি এ পর্যন্ত, সেগুলির ভূমিকা যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁদের একজনের নামও মনে করতে পারছি না। তাঁরা কী লিখেছিলেন ভূমিকাতে, মনে নেই তা-ও। এই ভাবনাটি মাথায় আসতেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম, চিন্তাও অদৃশ্য হয়ে গেল। বস্তুত, কলকাতা পুলিশের ফেসবুক পেজে এবং ওয়েবসাইটে ‘রহস্য রবিবার’ সিরিজের লেখাগুলি প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠকমহলে যে ‘ঝড়’ উঠেছিল, তার প্রতিক্রিয়ায় সংকলনটি প্রকাশ করতে একরকম বাধ্যই হয়েছি আমরা। লিখনশৈলীর বিষয়ে পাঠপ্রতিক্রিয়া ছিল অভূতপূর্ব। এবং সত্যি বলতে, লেখাগুলি একবার পড়তে শুরু করলে শেষ না করে উপায় থাকে না। এটা কম কৃতিত্বের নয়, কারণ কাহিনিগুলি সত্য ঘটনানির্ভর, লেখকের বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা ছিল না তথ্য এবং তদন্তের দিশা থেকে বিচ্যুত হওয়ার। শুধু লিখনশৈলীই নয়, আলোচিত মামলাগুলি কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দাদের পরিশ্রম ও দক্ষতার এক প্রামাণ্য নিদর্শন। এঁরা কেউ কল্পনার Sherlock Holmes বা Hercule Poirot নন, কিন্তু সামগ্রিক বিচারে এঁদের রহস্যভেদের ক্ষমতা এবং তদন্তের দক্ষতা বিশ্বের সেরা পুলিশবাহিনীগুলির সঙ্গে তুলনীয়।
যে বাহিনীতে এমন দুঁদে গোয়েন্দারা রয়েছেন, রয়েছেন সুপ্রতিম সরকারের মতো ক্ষমতাধর লেখক, সেই বাহিনীর নেতৃত্ব দেওয়া বিরল সম্মানের। কলকাতা পুলিশের অফিসারদের পেশাদারিত্ব নিয়ে আমার কখনই কোনও সংশয় ছিল না। তবে এটা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, সুপ্রতিমের লিখনশৈলী আমার কাছে ছিল সানন্দ বিস্ময়ের মতো। স্বাদু লেখনিতে গোয়েন্দাদের অনন্য দক্ষতার কাহিনি পাঠকমহলে বিপুল সমাদর পাবে বলেই আমার বিশ্বাস।
রহস্যভেদের কাহিনির সমাবেশ যে বইয়ে, তার ভূমিকা শেষ করা যাক রহস্য দিয়েই। পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি আজ থেকে ঠিক ৬৯ বছর আগের একটি খুনের মামলার প্রতি, যার কিনারা আজ পর্যন্ত হয়নি। ঘটনাটি ঘটেছিল অন্য মহাদেশে, অস্ট্রেলিয়ায়। ১৯৪৮ সালের ১ ডিসেম্বর এক অজ্ঞাতপরিচয় ‘Caucasian’ পুরুষের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়। শনাক্তকরণের মতো কোনও চিহ্ন ছিল না দেহে। ট্রাউজারের পকেটে শুধু পাওয়া গিয়েছিল ওমর খৈয়ামের বিখ্যাত বই ‘রুবাইয়াৎ’–এর একটি ছেঁড়া পাতা। যাতে লেখা ছিল ‘তামাম শুদ’ (এটি একটি পারস্যদেশীয় শব্দ, যার মানে ‘শেষ হওয়া’)। পাঠকরা নিশ্চয়ই পরিচিত ‘কাম তামাম’ শব্দ দুটির সঙ্গে, যা হিন্দিতে বহুলব্যবহৃত, এবং যা ‘খুন’-এর ইঙ্গিতবাহী।
খুিন এক্ষেত্রে পেশাদারি দক্ষতায় মৃতদেহের পরিধান থেকে মুছে দিয়েছিল শনাক্তকরণের সমস্ত সম্ভাব্য চিহ্ন। এই মামলাটি অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে জটিল হত্যারহস্য হিসাবে খ্যাত। প্রচলিত ধারণা, খুনটি হয়েছিল কোনও অজানা বিষের প্রয়োগে। ‘রুবাইয়াৎ’-এর যে সংস্করণটির ছেঁড়া পাতা পাওয়া গিয়েছিল মৃতের ট্রাউজারের পকেটে, সেটি তদন্তকারীরা খুঁজে বের করেছিলেন। বইটিতে একটি সংকেত লেখা ছিল, যার মর্মোদ্ধার আজ পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। অস্ট্রেলিয়ার পুলিশ তো বটেই, শিক্ষাজগতের গুণীজনের বহু বছরের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও। সংকেতটির অর্থ উদ্ধার করলে তবেই খুনির পরিচয় জানা সম্ভব, সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিল পুলিশ।
সংকেতটি তুলে দিলাম নীচে। রহস্যরসিক পাঠক চেষ্টা করে দেখতে পারেন মর্মার্থ উদ্ধারের।
‘গোয়েন্দাপীঠ লালবাজার’ আপনাদের ভাল লাগবে, আশা রাখি।
রাজীব কুমার আই.পি.এস.
নগরপাল, কলকাতা
১ ডিসেম্বর, ২০১৭
.
লেখকের কথা
শুরুতেই বলে নিই, এ বই কোনও নির্দিষ্ট পূর্বপরিকল্পনার পরিণতি নয়। কলকাতা পুলিশের জনপ্রিয় ফেসবুক পেজে পাঠক-পাঠিকাদের অনেকে অনুরোধ করেছিলেন, পুরনো কিছু মামলা নিয়ে লিখতে, যার কিনারায় সাফল্য পেয়েছিল পুলিশ।
নগরপাল শ্রীরাজীব কুমারকে জানালাম একদিন, গত বছরের জুলাইয়ের শেষাশেষি। শুনেই এক কথায় রাজি, ‘গুড আইডিয়া, লেখো, কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ঐতিহ্যের কথা লিপিবদ্ধ থাকা তো উচিতই। লেখো।’
এ বইয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন নগরপালের উৎসাহবাক্যেই, তাঁরই প্রেরণায়। প্রতি রবিবার আমাদের ফেসবুকের পাতায় ‘রহস্য রবিবার’ শীর্ষকে পোস্ট হতে থাকল সাড়া-জাগানো কিছু পুরনো খুনের মামলার ইতিবৃত্ত। সাইবার-দুনিয়ার পাঠক-পাঠিকাদের প্রশ্রয় এবং সমর্থনে একের পর দুই, চারের পর পাঁচ, নয়ের পর দশ। লেখাগুলি বাঁধা পড়ুক দুই মলাটে, বই হোক, অনুরোধ এল অনেক। সেই অনুরোধকে শিরোধার্য করেই তড়িঘড়ি এই বইয়ের প্রস্তুতি এবং প্রকাশ।
পাঠকহৃদয়ে গোয়েন্দাকাহিনির আকর্ষণ চিরকালীন, লেখা বাহুল্য। হেমেন্দ্রকুমারের জয়ন্ত-মানিক বা নীহাররঞ্জনের কিরীটি, শরদিন্দুর ব্যোমকেশ বা সত্যজিতের ফেলুদা, কাহিনি এবং তার কুশীলবরা কল্পনার। লেখক স্বাধীনভাবে রহস্যের ঘনঘটা তৈরি করেন বিবিধ উপাদানে। এই বইয়ের কাহিনিগুলি চরিত্রে ভিন্ন। গোয়েন্দারা বাস্তবের, চরিত্ররা রক্তমাংসের এবং কাহিনি ‘গল্প হলেও সত্যি’-র শ্রেণিভুক্ত। যা ঘটেছিল আর যেভাবে ঘটেছিল, সেই লক্ষ্মণরেখার বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই কোনও।
কলকাতা পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ইতিহাস শতাব্দীপ্রাচীন, পত্তন ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে, ১৮৬৮ সালে। সর্বজনবিদিত তথ্য, কলকাতা পুলিশকে তুলনা করা হত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে, দেশব্যাপী এতটাই সুনাম ছিল গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারদের। এবং এই সুনাম অর্জিত হয়েছিল অগণিত জটিল মামলার রহস্যভেদে ধারাবাহিক পেশাদারি দক্ষতায়। সেই মামলাগুলির থেকে বারোটি বেছে নিয়ে এই বইয়ে সংকলিত রইল তদন্তের নেপথ্যকথা। প্রতিটি মামলাই খুনের। প্রতিটিই কলকাতা পুলিশের ইতিহাসে দিকচিহ্ন, হয় অপরাধীর বেনজির ভাবনায় বা পদ্ধতিতে, নয় তদন্তকারী অফিসারের নৈপুণ্যের মানদণ্ডে, কিংবা অভিযুক্তকে শাস্তিদানে বিজ্ঞানমনস্কতার বিরল প্রয়োগে।
আলোচিত মামলাগুলির সময়কাল পাঠক লক্ষ করবেন নিশ্চিত । বিংশ শতকের তিরিশের দশকের ঘটনা দিয়ে শুরু। শেষ মাত্র দশ বছর আগে ঘটে যাওয়া হত্যাকাণ্ডে। যা প্রমাণ করে, কলকাতা পুলিশের রহস্যভেদের দক্ষতার ‘সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে’, এবং বাস্তবের ফেলু-ব্যোমকেশদের ধারাবাহিক কীর্তিতেই লালবাজার হয়ে উঠেছে গোয়েন্দাপীঠ।
জটিল খুনের মামলার তদন্ত অনেকাংশে তুলনীয় টেস্ট ক্রিকেটের সঙ্গে। একদিনের ম্যাচ নয়, কুড়ি-বিশের বিনোদন তো নয়ই। ঘটে যাওয়া অপরাধের কিনারা করা সিঁড়ির প্রথম ধাপ মাত্র। সাক্ষ্যপ্রমাণ সংহত করে ঠাসবুনোট চার্জশিট পেশ করার পরও অসমাপ্ত থাকে কাজ। দীর্ঘ বিচারপর্বে অভিযুক্তের শাস্তিবিধান নিশ্চিত করতে পারলে তবেই বৃত্ত সম্পূর্ণ হয় তদন্তের। রোম্যান্স-রোমাঞ্চ বর্জিত এই পথ পাড়ি দিতে অশেষ ধৈর্যের প্রয়োজন হয় তদন্তকারী অফিসারের। প্রয়োজন হয় শত প্রতিকূলতাতেও ক্রিজ়ে দাঁত কামড়ে পড়ে থাকার অধ্যবসায় এবং মনোসংযোগের। পাঁচ দিনের ক্রিকেটের মতো।
বাস্তবের সত্যান্বেষীদের সেই কর্মকাণ্ডই এই বইয়ের আধার। বাস্তবের অপরাধের তদন্তের আখ্যান বাংলা ভাষায় একেবারেই অমিল, এমন নয়, কিন্তু তদন্তপদ্ধতির সামগ্রিকতার প্রামাণ্য দলিল চোখে পড়ে না বড় একটা। সে অভাব যদি কিছুটাও দূর করতে পারে বইটি, তদন্তশিক্ষার্থীরা যদি কিছুমাত্রও উপকৃত হন আগামীতে, পরিশ্রম সার্থক।
লেখাগুলির সময়কাল গত বছরের জুলাইয়ের শেষ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত। যে সময়টা কলকাতা পুলিশের অ্যানুয়াল পরীক্ষা, যে সময়টা শারদোৎসবের। পরীক্ষার প্রস্তুতির মধ্যেও লেখা গিয়েছে নগরপালের সোৎসাহ প্রশ্রয়ে। তাঁকে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানানোর ধৃষ্টতা নেই, শ্রদ্ধা জানাই।
ধন্যবাদ প্রাপ্য ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার শ্রীঅতনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের, যিনি মামলাগুলির তথ্যতালাশে নিরলস পরিশ্রম করেছেন। ধন্যবাদ অবসরপ্রাপ্ত অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার নীহারেন্দু রায়কে, যিনি আক্ষরিক অর্থেই কলকাতা পুলিশের ‘সিধু জ্যাঠা’, যিনি সরবরাহ করেছেন এই বইয়ে ব্যবহৃত দুর্মূল্য নথিপত্র। স্নেহভাজন সহকর্মী ইন্দ্রজিৎ দত্ত-কে ধন্যবাদ, ম্যানুস্ক্রিপ্ট টাইপ করায় হাসিমুখে অক্লান্ত থাকার জন্য।
বিনিদ্র রাতে যখন লিখেছি পেশার ব্যস্ততম সময়ে, পারিবারিক দায়দায়িত্ব একপ্রকার বিসর্জন দিয়েই, আগাগোড়া পাশে থেকেছে স্ত্রী ঋতুপর্ণা, যার সমর্থন না পেলে এই বই দিনের আলো দেখত না।
ছোটবেলা থেকে এদিক-ওদিক অকিঞ্চিৎকর লেখালেখি যতটুকু, দিশারী ছিলেন মা-বাবা। কেউই বেঁচে নেই। তবে যেখানেই থাকুন, জানি, পড়ছেন।
১ জানুয়ারি, ২০১৮
কলকাতা
১.০১ এভাবেও মেরে ফেলা যায়!
[পাকুড় হত্যামামলা
তদন্তকারী অফিসার এম এল রহমান]
উফফ, কী একটা ফুটিয়ে দিয়ে চলে গেল!
পাঞ্জাবির হাতা ততক্ষণে গুটিয়ে ফেলেছেন বছর কুড়ির যুবক। পরীক্ষা করছেন ডান হাতের উপরের দিকের ক্ষতচিহ্ন। পিন ফোটালে যেমন হয়। জ্বালা করছে বেশ।
সে বহুকাল আগের কথা। বেলা আড়াইটে তখন। হাওড়া স্টেশনের গড়পড়তা দুপুর দ্রুত রওনা দিচ্ছে বিকেলের দিকে। ভারী ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গিতে। ভিড়ে হাঁসফাঁস স্টেশন-চত্বর। যাত্রীদের লটবহর কাঁধে কুলিদের ‘থোড়া সাইড দিজিয়েগা ভাইসাব!’ মন ভাল বা খারাপ করে দেওয়া কু-ঝিকঝিক রেলগাড়ির। ইঞ্জিন থেকে চলকে ওঠা ধোঁয়া পাক খেতে খেতে ঊর্ধ্বমুখী। অমুক নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে তমুক ট্রেন একটু পরেই পাড়ি দেবে গন্তব্যে, ঘোষণা মিনিটে মিনিটে।
সন ১৯৩৩। তারিখ ২৬ নভেম্বর। স্টেশনের চলতিফিরতি ভিড়ের নজর কাড়ছে পাকুড়ের জমিদারবাড়ির কনিষ্ঠ পুত্র অমরেন্দ্রচন্দ্র পান্ডের ঘরে ফেরার আয়োজন। পাত্রমিত্র-অমাত্যের দঙ্গল এসেছে স্টেশনে। ছোটখাটো শোভাযাত্রাই বলা চলে। অমরেন্দ্রর সঙ্গে যাবেন সহোদরা বনবালা। বিশেষ ঘনিষ্ঠ কমলাপ্রসাদ পান্ডে, অশোক প্রকাশ মিত্র এবং আরও অনেকে এসেছেন বন্ধুকে ছাড়তে। বৈমাত্রেয় দাদা বিনয়েন্দ্রও উপস্থিত।
ট্রেন ছাড়ব-ছাড়ব করছে, অমরেন্দ্র-বনবালাকে ঘিরে জটলা। বিদায়-সম্ভাষণের পালা চলছে। হঠাৎই উলটো দিক থেকে একটি লোক, গায়ে খদ্দরের ময়লা চাদর, দ্রুতপায়ে হেঁটে এসে অমরেন্দ্রকে হালকা ধাক্কা দিয়ে, কেউ কিছু বোঝার আগেই নিমেষে মিলিয়ে গেল ভিড়ে। আর অমরেন্দ্রর মুখ থেকে ছিটকে বেরল যন্ত্রণা, উফফ, কী একটা ফুটিয়ে দিয়ে চলে গেল!
আজ যে মামলার কথা, যখনকার কথা, পাঠক-পাঠিকাদের সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্মই হয়নি, নিশ্চিত। প্রায় পঁচাশি বছর আগের ঘটনা এই মামলা বিরলতমের পর্যায়ভুক্ত। আজও আলোচিত হয় দেশ-বিদেশের অপরাধ-বিষয়ক লেখালেখিতে, গবেষণায়। বলা হয়, “One of the first cases of individual bioterrorism in modern world history.” কী বাংলা হয়? জীবাণু-অস্ত্রে ব্যক্তিহত্যা? জুতসই হল না মোটেই। না হোক, ঘটনার বিবরণে আসি, যা পড়লে মনে হতে বাধ্য, এভাবেও মেরে ফেলা যায়!
পাকুড় হত্যা মামলা। টালিগঞ্জ থানা, কেস নম্বর ৬৭। ধারা, ভারতীয় দণ্ডবিধির তারিখ ১৭/২/৩৪। ৩০২/১২০ বি। খুন এবং অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র। অনেকে শুনেছেন এই মামলার কথা, বিস্তর লেখাও হয়েছে এ নিয়ে। ইন্টারনেটেও পাবেন। তবে অধিকাংশ বিবরণেই নানা ভাষা-নানা মত-নানা অনুমান। বিভ্রান্তির অবকাশ অনেক। রইল প্রামাণ্য ঘটনাপ্রবাহ, কেস ডায়েরি থেকে, সযত্নে যা রক্ষিত আছে উত্তর কলকাতার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডে আমাদের সংগ্রহশালায়।
পাকুড় মামলার চার্জশিটের প্রতিলিপি
পাকুড়ের অবস্থান ঝাড়খণ্ডের উত্তর-পূর্বে। সাঁওতাল পরগনায়। বহুদিন সাহেবগঞ্জ জেলার প্রশাসনিক কেন্দ্রস্থল ছিল। স্বতন্ত্র জেলার মর্যাদা মিলেছে ’৯৪-এ। দেশের মানচিত্রে পাকুড় বিখ্যাত ব্ল্যাকস্টোনের জন্য। উত্তরে সাহেবগঞ্জ, দক্ষিণে দুমকা, পশ্চিমে গোদ্দা জেলা আর পূর্বে আমাদের মুর্শিদাবাদ-বীরভূম। প্রাক-স্বাধীনতা আমলে দেশের অন্যতম ধনাঢ্য জমিদারির মালিকানা ছিল পাকুড়ের পান্ডে পরিবারের। সমসময়ের বংশলতিকার যেটুকু প্রয়োজন কাহিনির স্বার্থে, বলে নিই।
কুমার প্রতাপেন্দ্রচন্দ্র পান্ডের দুই স্ত্রী ছিলেন। দু’জনেই পরলোকগতা। প্রথম পক্ষের পুত্র বিনয়েন্দ্র, কন্যা কাননবালা। এক পুত্র, এক কন্যা দ্বিতীয় পক্ষেও। অমরেন্দ্র আর বনবালা। প্রতাপেন্দ্রর দাদা গত হয়েছেন, যাঁর নিঃসন্তান স্ত্রী বর্তমান। রানি সূর্যবতীদেবী। অমরেন্দ্রর মাতৃবিয়োগ হয়েছিল জন্মের বছরদুয়েকের মধ্যেই। সন্তানহীনা সূর্যবতী মাতৃস্নেহে লালন করেছিলেন শিশু অমরেন্দ্রকে।
কুমার প্রতাপেন্দ্র আর রানি সূর্যবতীর মধ্যে সমান ভাগাভাগি হয়েছিল জমিদারির বিষয়সম্পত্তি। জমিদারির বার্ষিক আয় ছিল লাখখানেকের ঢের বেশি। সে-যুগের নিরিখে কুবেরের বিষয়-আশয় প্রায়।
প্রতাপেন্দ্র মারা গেলেন ১৯২৯-এ। অমরেন্দ্র ও বিনয়েন্দ্রর মধ্যে সম্পত্তির সমবণ্টন করে গিয়েছিলেন উইলে। অমরেন্দ্র তখনও নাবালক, বছর পনেরোর কিশোর। স্কুলের পাঠ শেষ করবেন কিছুদিনের মধ্যে। বিনয়েন্দ্রর বয়স তখন বাইশ, দায়িত্ব ছিল সম্পত্তির দেখাশোনার।
বিনয়েন্দ্র ছিলেন ইন্দ্রিয়সুখে আচ্ছন্ন মানুষ। জীবনদর্শন সহজ, “মেজাজটাই তো আসল রাজা, আমি রাজা নয়।” নানাবিধ দুর্লক্ষণ ছিল মেজাজের। দিনরাতের অধিকাংশ সময় ‘জলপথেই’ থাকতে পছন্দ করতেন। উদ্দাম নারীসঙ্গ স্বভাবগত, নিয়মিত নিশিযাপন বালিকাবালা এবং চঞ্চলা নামে দুই রক্ষিতার সাহচর্যে। প্রমোদবিলাসে মাঝেমধ্যে পাড়ি দিতেন বোম্বাই। রুপোলি পরদার রংবাহারে বরাবরের আকর্ষণ। সংযম এবং শৃঙ্খলা, দুইয়ের সঙ্গেই সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন কৈশোরেই।
অমরেন্দ্র ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা। ভদ্র, নম্র, পারিবারিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী। উচ্চশিক্ষায় আগ্রহী, নিয়মিত শরীরচর্চাও করেন। স্বভাবগুণে প্রবল জনপ্রিয় প্রজাকুলে। ‘ছোটবাবু’ বলতে অজ্ঞান পাকুড়ের আবালবৃদ্ধবনিতা।
স্কুলের পাট চুকিয়ে অমরেন্দ্র ভরতি হলেন পাটনা কলেজে। পড়াশুনোর খরচ নিয়মিত পাঠাতেও প্রায়ই গড়িমসি করতেন বিনয়েন্দ্র। অমরেন্দ্র আঠারোর চৌকাঠে পা দিলেন ফোর্থ ইয়ারে এবং সাবালকত্ব প্রাপ্তির পরই সম্পত্তির অংশের দায়িত্ব বুঝে নিতে চিঠি লিখলেন বিনয়েন্দ্রকে।
সেটা ১৯৩২ সাল। রানি সূর্যবতী থাকতেন দেওঘরে, সব খবরই পেতেন বিনয়েন্দ্রর টালমাটাল জীবনধারার। তিনিও পরামর্শ দিলেন অমরেন্দ্রকে, যথাসম্ভব দ্রুত বিষয়সম্পত্তি বুঝে নেওয়ার।
মাত্রাছাড়া ভোগবিলাসে অবধারিত টান পড়বে, তাই বৈমাত্রেয় ভাইকে তার প্রাপ্য অংশ দিয়ে দেওয়ায় বিনয়েন্দ্রর অনীহা ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু আইন তো আর অনীহার অনুগত নয়, অমরেন্দ্রকে বুঝিয়ে দিতে হল প্রাপ্য অর্ধাংশ। এবং হস্তান্তরের প্রক্রিয়ায় দুই ভাইয়ের মধ্যে যথেষ্ট তিক্ততা উৎপন্ন হল। বিস্তর চিঠিচাপাটি, তপ্ত বাক্যবিনিময়, সব।
পুজোর ছুটিতে অমরেন্দ্র বেড়াতে গেলেন দেওঘরে, রানি সূর্যবতীর কাছে। বিনয়েন্দ্রও এলেন কিছুদিন পরে। উঠলেন দেওঘরেরই অন্যত্র, বাড়ি ভাড়া করে। এক সন্ধেয় বিনয়েন্দ্র বললেন, চল বাবু (অমরেন্দ্রর ডাক নাম), একটু বেড়িয়ে আসি। বেরনো হল সান্ধ্যভ্রমণে। হঠাৎই বিনয়েন্দ্র বললেন, ‘তোর জন্য একটা জিনিস এনেছি কলকাতা থেকে। এই দ্যাখ।’ বলেই পকেট থেকে বার করলেন শৌখিন নাকে-আঁটা চশমা (Pince-nez glasses)। একরকম জোর করেই পরিয়ে দিলেন ভাইকে। পরানোর সময় নাকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশিই ব্যথা পেলেন অমরেন্দ্র। ছড়েও গেল একটু।
নাকে চাপটা কি একটু বেশিই দিয়েছিল দাদা? একটু খটকা যে লাগেনি অমরেন্দ্রর, এমনটা নয়। বন্ধুদের জানিয়েওছিলেন, বলেছিলেন সূর্যবতীকেও। সকলেই কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ করেছিলেন শুনে। অস্বস্তি আশঙ্কায় পরিণত হল, যখন দিন তিনেক পরে মুখের একটি দিক ফুলে গিয়ে প্রায় অবশ হয়ে গেল অমরেন্দ্রর।
বিনয়েন্দ্র তার আগেই ফিরে এসেছেন কলকাতায়। পারিবারিক চিকিৎসককে খবর দেওয়া হল। তিনি দেখেশুনে বললেন, টিটেনাসের সংক্রমণ। Anti-tetanus প্রতিষেধক চালু হল প্রথামাফিক।
চিকিৎসা চলাকালীনই বিনয়েন্দ্র দেওঘরে পাঠালেন তাঁর পরিচিত এক তরুণ ডাক্তারকে। নাম তারানাথ ভট্টাচার্য, কথাবার্তায় চৌকস। এসেই প্রস্তাব দিলেন মরফিন ইঞ্জেকশন দেওয়ার। ততদিনে দেওঘরের একাধিক চিকিৎসক দিনরাত পর্যবেক্ষণে রেখেছেন অসুস্থ অমরেন্দ্রকে। কেউই মানলেন না তারানাথের পরামর্শ।
বিনয়েন্দ্র ছিলেন গভীরতম জলের মাছ। নিজেই চলে এলেন দেওঘর, সঙ্গে তুলনায় অভিজ্ঞ এক চিকিৎসক, ডাক্তার দুর্গারতন ধর। যিনি চিকিৎসাবিদ্যার ব্যাপারে প্রভূত জ্ঞান বিতরণ করে চিকিৎসকদের রাজি করিয়ে ফেললেন একটি ইঞ্জেকশন দিতে। যেটি নিজেই সঙ্গে করে এনেছেন কলকাতা থেকে। দেওয়া হল ইঞ্জেকশন।
কলকাতায় রোগী দেখার জরুরি প্রয়োজনের অজুহাতে ডা. ধর আধঘণ্টা পরে কলকাতার ট্রেন ধরলেন। সঙ্গী বিনয়েন্দ্রও। এদিকে ইঞ্জেকশন দেওয়ার ঘণ্টাখানেক পরই আচমকা দ্রুত শারীরিক অবনতি হতে শুরু করল অমরেন্দ্রর। প্রায় অচৈতন্য, রক্তচাপ যখন-তখন অগ্রাহ্য করছে বিপদসীমা। ‘এই যায় সেই যায়’ অবস্থা। সে যাত্রা কোনওক্রমে সামাল দিলেন ডাক্তাররা।
কয়েকদিন পর বিনয়েন্দ্র ফের উদয় হলেন দেওঘরে, ভাই কেমন আছে দেখার অছিলায়। সঙ্গে এবারও সেই ডাক্তার ধর এবং আরও একজন। ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য। ঢের শিক্ষা হয়েছে ততদিনে অমরেন্দ্রর বন্ধুবান্ধব-শুভানুধ্যায়ীদের। সূর্যবতীও কড়া নির্দেশ জারি করেছেন বিনয়েন্দ্রকে দেওঘরের বাড়িতে ঢুকতে না দেওয়ার। দেওয়া হলও না। নিষ্ফলা বাদানুবাদের পর বিনয়েন্দ্র দুই সঙ্গী-চিকিৎসক সহ ফিরে গেলেন কলকাতায়।
অমরেন্দ্রর শরীরস্বাস্থ্য চিন্তায় ফেলল সূর্যবতীকে। যে ছেলের ছোটবেলার অভ্যেস ভোর পাঁচটায় উঠে শরীরচর্চার, সে বেলা দশটার আগে এখন বিছানাই ছাড়তে পারে না দুর্বলতার জেরে। বছর ঘুরে তখন ১৯৩৩। অমরেন্দ্রকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হল সুচিকিৎসার প্রয়োজনে। হরিশ মুখার্জি রোডের একটি বিশাল বাড়ি ভাড়া করা হল। খবর দেওয়া হল সেই কিংবদন্তি চিকিৎসককে, যাঁর নামে কলকাতার এনআরএস মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। সর্বজনশ্রদ্ধেয় ডা. নীলরতন সরকার রোগী দেখে ওষুধপত্র দিলেন। সঙ্গে পরামর্শ, কিছুদিন কাজকর্মের চিন্তা সম্পূর্ণ দূরে রেখে বাইরে কোথাও থেকে ঘুরে আসার।
অমরেন্দ্র ‘চেঞ্জে’ গেলেন ভুবনেশ্বরে, কিন্তু অবস্থার তেমন উন্নতি হল না। মাথা ঘোরে, অল্পেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। খিদে কমে গিয়েছে। বই পড়তে ভালবাসতেন খুব, সে ইচ্ছেও যেতে বসেছে। বন্ধুরা নতুন বই পাঠালে দু’-চার পাতা উলটেই রেখে দেন। মাসকয়েক পর ভুবনেশ্বর থেকে ফিরে এলেন পাকুড়ে। ভগ্ন শরীরেই জমিদারির কাজকর্ম দেখাশোনা শুরু করলেন সাধ্যমতো।
বিনয়েন্দ্র এ সময়টা শান্তশিষ্ট দিনযাপন করছিলেন, ভাবার কারণ নেই কোনও। দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না, ছকেরও না। চক্রান্তের শেষ অঙ্ক অভিনীত হল ’৩৩ -এর নভেম্বরে। ১৮ তারিখ পাকুড়ের বাড়িতে সূর্যবতীদেবীর টেলিগ্রাম এল অমরেন্দ্রর নামে, ‘কলকাতায় শীঘ্র আসিও। রাজস্ব-সংক্রান্ত আইনি আলোচনা রহিয়াছে।’
পত্রপাঠ কলকাতা রওনা দিলেন অমরেন্দ্র এবং গিয়ে আবিষ্কার করলেন, টেলিগ্রামটি ভুয়ো। সূর্যবতী আদৌ আসেননি কলকাতায়। তারবার্তাটি তাঁর নয়।
অমরেন্দ্র সব জানালেন সূর্যবতীকে। দু’জনেই সহমত হলেন, এ অপকর্ম বিনয়েন্দ্রর। জ্যাঠাইমা সূর্যবতী আদরের ‘বাবু’-কে সতর্ক করে দিলেন, ‘কাছেপিঠে ঘেঁষতে দিবি না দাদাকে।’ অমরেন্দ্র সরাসরি জানতে চাইলেন দাদার কাছে টেলিগ্রামের ব্যাপারে। বিনয়েন্দ্র অম্লানবদনে অস্বীকার করলেন। এরই মধ্যে বিনয়েন্দ্র একাধিকবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন দুই পুত্রের জয়েন্ট অ্যাকাউন্টে প্রতাপেন্দ্রর রেখে যাওয়া দু’লাখ টাকার সিংহভাগ অমরেন্দ্রর অজ্ঞাতে সই জাল করে তুলে নেওয়ার। সবই জানতে পেরেছিলেন অমরেন্দ্র পারিবারিক উকিলের মাধ্যমে। সে নিয়েও বচসা হল খানিক।
২৫ নভেম্বর, ১৯৩৩। পরের দিন অমরেন্দ্রর কলকাতা থেকে পাকুড়ে ফিরে যাওয়ার কথা দুপুরের ট্রেনে। সন্ধেবেলা অমরেন্দ্রর কলকাতার অস্থায়ী বাসস্থানে এসে হাজির বিনয়েন্দ্র। সব তিক্ততা ভুলে গিয়ে হঠাৎই যেন স্নেহশীল বড়দার ভূমিকায়। কথায় কথায় স্মৃতিচারণ করছেন শৈশব-কৈশোরের, কিঞ্চিৎ ঘনঘনই গলা বুজে আসছে কান্নায়, ‘তুই আমাকে ভুল বুঝিস না বাবু, শরীরের যত্ন নিস ভাই।’
অমরেন্দ্র দাদার চরিত্র জানতেন, কুম্ভীরাশ্রুতে বিচলিত হওয়ার কারণ দেখলেন না কোনও। বিনয়েন্দ্র যাওয়ার আগে কথায় কথায় জেনে নিলেন, পরদিন ভাইয়ের ট্রেন কখন।
২৬ নভেম্বর। স্টেশনে অমরেন্দ্র এবং আত্মীয়বান্ধবরা একটু অবাকই সহাস্য বিনয়েন্দ্রকে দেখে। কেউ কেউ বললেনও, এ আপদ এখানে কেন? অমরেন্দ্র নিরস্ত করলেন উত্তেজিত স্বজনদের। যতই কুচক্রী হোন, বৈমাত্রেয় হলেও দাদা তো! স্টেশনে এসেছেন, ও ভাবে বিদেয় করে দেওয়া যায়? এর কিছু পরে অতর্কিতে উলটোদিক থেকে খদ্দরের চাদরমুড়ি অপরিচিতের দ্রুত ধাক্কা দিয়ে অন্তর্ধান, গাড়ি ছাড়ার পূর্বমুহূর্তের সে ঘটনা বলেছি শুরুতে।
পাঞ্জাবির হাতা তুলে অমরেন্দ্র দেখালেন ক্ষতচিহ্ন। আপাতদৃষ্টিতে মারাত্মক কিছু নয়। কিছুটা তরল পদার্থ পিন ফোটানোর জায়গা থেকে চুঁইয়ে পড়েছে পাঞ্জাবিতে। ট্রেন ছাড়তে তখন বাকি মিনিট পাঁচেক। সহোদরা বনবালা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। অমরেন্দ্রর বন্ধু কমলাপ্রসাদ এবং অন্যরাও। বললেন, ডাক্তার দেখিয়ে নেওয়া যাক। দু’দিন পরই না হয় পাকুড় যাওয়া যাবে। বিনয়েন্দ্রও কপট উদ্বেগ দেখালেন প্রাথমিক, তারপর বললেন, ‘এ তো সামান্য ব্যাপার, পাকুড়ে গিয়েও তো ডাক্তার দেখিয়ে নেওয়া যায়।’ কমলাপ্রসাদ প্রতিবাদ করতে গেলে বিনয়েন্দ্র মেজাজ হারালেন, ‘আমরা পাকুড়ের জমিদারবাড়ির। এসব তুচ্ছ ব্যাপারে তোমরা সাধারণরা মাথা ঘামাতে পারো। আমরা নয়।’
অমরেন্দ্রর কিছু জরুরি কাজও ছিল পরের দু’দিনে। ভাবলেন, ডাক্তার দেখিয়ে নেব বাড়ি ফিরে। বনবালাকে নিয়ে উঠে বসলেন পাকুড়গামী ট্রেনে। এবং মারাত্মক ভুল করলেন।
ভাইবোন যখন ট্রেনে বিকেলের জলযোগ সারছেন, কথোপকথন হল এইরকম।
—দাদাভাই, আমার কিন্তু ব্যাপারটা ভাল ঠেকছে না।
—কেন রে?
—না, ওই পিন ফোটানোর ব্যাপারটা । মনটা খচখচ করছে।
—ও কিছু না। পকেটমার-টার হবে। ছোট ক্ষুরটুর ছিল হয়তো হাতে।
—ক্ষুরে অমন দাগ হয়? আমি লোকটাকে আগে কোথায় যেন দেখেছি, মনে করতে পারছি না কিছুতেই …
—যাহ্, কী যে বলিস। তুই আবার কোথায় দেখলি?
—না রে, দেখেছি কোথাও, একদম এক চেহারা।
—চেহারাটা তো আমিও দেখলাম। বেঁটে, মিশকালো, গায়ে খদ্দরের চাদর ছিল। পায়ে চপ্পল।
—দাদাভাই! মনে পড়েছে! আমরা গত সপ্তাহে যখন পূর্ণ থিয়েটারে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম, ওই লোকটা টিকিট কাউন্টারের সামনে ঘোরাঘুরি করছিল।
—আরে ধুর। তোর মনের ভুল। বেশি ভাবিস না তো।
বনবালার আশঙ্কা যে অমূলক ছিল না, তা বোঝা গেল পরের দিন থেকেই। প্রবল অসুস্থ হয়ে পড়লেন অমরেন্দ্র। ২৮ তারিখ রাতে ফিরিয়ে আনা হল কলকাতায়। এবার উঠলেন রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের একটা ভাড়াবাড়িতে। ডাকা হল আর এক প্রবাদপ্রতিম চিকিৎসককে। ডা. নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত। অবস্থা দেখে ডাক্তারবাবু ‘ব্লাড কালচার’ করতে বললেন অবিলম্বে। ডান দিকের বাহুমূল ততক্ষণে ফুলে উঠেছে অমরেন্দ্রর। জ্বর নামছেই না ১০৫ ডিগ্রির নীচে। কষ্ট পাচ্ছেন প্রচণ্ড। রক্তচাপ হোক বা হৃদ্স্পন্দন, প্রতি ঘণ্টায় একটু একটু করে চলে যাচ্ছে নিয়ন্ত্রণের বাইরে।
৩ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় অমরেন্দ্র জ্ঞান হারালেন, ৪ ডিসেম্বর সকালে প্রাণ। ‘ব্লাড কালচার’-এর রিপোর্ট এল পরদিন। যার সারাংশ পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ডাক্তাররা। মৃতের রক্তে ‘Pasteurella Pestis’ ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ। যা শরীরে ঢুকলে plague-এ আক্রান্ত হওয়া অনিবার্য। প্লেগের মারণছোবলেই প্রাণনাশ অমরেন্দ্রর, সংশয়ের অবকাশ নেই তিলমাত্র।
রোগভোগে আপাত-স্বাভাবিক মৃত্যু। ময়নাতদন্ত হল না, দাহ হল নিয়মমাফিক। মুখাগ্নি করলেন বিনয়েন্দ্র, কেঁদে ভাসালেন। ওই কুনাট্য সহ্য করতে হল অমরেন্দ্রর ঘনিষ্ঠদের। যাঁদের আগাগোড়াই সন্দেহ ছিল বিনয়েন্দ্রর উপর। পিন ফোটানোর ঘটনা নিশ্চয়ই বিনয়েন্দ্ররই মস্তিষ্কপ্রসূত, দৃঢ় বিশ্বাস ছিল অমরেন্দ্রর বন্ধুদের। কিন্তু প্রমাণ কই? সন্দেহের বশে তো আর কাউকে ফাঁসিকাঠে চড়ানো যায় না।
স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন করা এক যুবকের অকালমৃত্যু, তা-ও প্লেগে! চিন্তায় পড়ে গেলেন কলকাতার চিকিৎসকমহল। দিকপাল ডাক্তাররা শেষ সময়ে চিকিৎসা করেছিলেন, কথা বলেছিলেন অমরেন্দ্রর আত্মীয়বন্ধুদের সঙ্গে, নথিবন্দি করেছিলেন দিনকয়েক আগের পিন ফোটার ঘটনা এবং পরবর্তী সমস্ত রোগলক্ষণ। গোলমাল আছে কিছু, চিকিৎসকদল আন্দাজ করেছিলেন দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায়।
ডাক্তাররা স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই ১২ ফেব্রুয়ারি একঝাঁক প্রশ্ন পাঠালেন ট্রপিক্যাল মেডিসিনের ডিরেক্টরের কাছে। প্লেগের ‘bacilli’ কি হাইপোডারমিক নিডলের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করানো যায়? গেলে কত পরিমাণে? যতটা যায়, ততটা কি প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর জন্য যথেষ্ট? এ ছাড়া আরও বেশ কিছু, টেকনিক্যাল খুঁটিনাটি। বিস্তারিত উত্তর এল চার দিন পর, ১৬ তারিখ। বলা হল, এই মৃত্যু অস্বাভাবিক, ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটানো হয়েছে। স্বাভাবিক নিয়মে এ জিনিস ঘটেনি। অতএব, ‘homicidal death’— খুন! এবং যে ‘bacilli’-ঘটিত মৃত্যু, তা কলকাতায় পাওয়া যায় না। একমাত্র বোম্বাইতেই (সেসময়ের নামটাই রাখলাম বাণিজ্যনগরীর) মেলে Haffkine Institute-এ।
অমরেন্দ্রর বন্ধুরা কিন্তু হাল ছাড়েননি দাহকার্য সাঙ্গ হওয়ার পরও। ট্রপিক্যালের রিপোর্ট আসার একমাস আগেই ঘটনার সবিস্তার বিবরণ সমেত কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দফতরের কর্তাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। সঙ্গে ছিলেন পাকুড় জমিদারবাড়ির পারিবারিক উকিল। অভিযোগ দায়ের করার মতো নথিপত্র ছিল না হাতে। তাই কেস নথিবদ্ধ করা হয়নি তখনও, কিন্তু পুলিশের গোপন অনুসন্ধান এবং নজরদারি চালু হয়েছিল বিনয়েন্দ্র এবং তারানাথের গতিবিধির উপর। গোয়েন্দারা নিয়মিত যোগাযোগ রাখছিলেন প্রাক্-মৃত্যু চিকিৎসা যাঁরা করেছিলেন, সেই ডাক্তারদের সঙ্গে। অলিখিত তদন্ত একরকম শুরুই হয়ে গিয়েছিল।
ডা. এন আর সেনগুপ্তকে পাঠানো সাক্ষীদানের সমন
১৬ ফেব্রুয়ারি ট্রপিক্যাল মেডিসিনের রিপোর্ট আসামাত্রই কমলাপ্রসাদ টালিগঞ্জ থানায় অভিযোগ দায়ের করলেন। পাঁচজন অভিযুক্ত। বিনয়েন্দ্রচন্দ্র পান্ডে, ডাক্তার তারানাথ ভট্টাচার্য, ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য, ডাক্তার দুর্গারতন ধর এবং সেই অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি, যে স্টেশনে পিন ফুটিয়েছিল।
FIR হয়েছে খবর পাওয়ামাত্র পালালেন বিনয়েন্দ্র। পালিয়ে যাবেন কোথায়, নজরদারি তো ছিলই অষ্টপ্রহর। গ্রেফতার করা হল সে-রাতেই। আসানসোল স্টেশনে, ট্রেনের কামরা থেকে। ডা. ধর ধরা পড়লেন পরের দিন, তারানাথ আরও একদিন পরে। ১৮ ফেব্রুয়ারির সকালে। ডাক্তার শিবপদ ভট্টাচার্য মাসখানেক পর, ২৪ মার্চ।
কিন্তু যে লোকটি পিন ফুটিয়েছিল? বেঁটে, কালো, খদ্দরের চাদরমুড়ি দেওয়া অপরিচিত? বিনয়েন্দ্র স্বীকার করলেন, তিনিই লোকটাকে পূর্ণ থিয়েটারে পাঠিয়েছিলেন অমরেন্দ্রকে চিনে নিতে। কিন্তু লোকটির নাম-ঠিকানা এক-একবার এক-একরকম বলে চললেন, কোথাও খোঁজ মিলল না হাজার চেষ্টাতেও। ছবি-টবি আঁকিয়ে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার পরেও না।
দুটো সম্ভাবনা ছিল। এক, প্রচুর টাকাপয়সা দিয়ে আততায়ীকে চলে যেতে বলেছিলেন বিনয়েন্দ্র ভিনরাজ্যের কোনও প্রত্যন্ত এলাকায়, যেখান থেকে খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য। দুই, ঘটনার পর বিনয়েন্দ্রই লোক লাগিয়ে পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দিয়েছিলেন আততায়ীকে। যাতে ভবিষ্যতে ব্ল্যাকমেলের আশঙ্কাও নির্মূল করে দেওয়া যায় চিরতরে। দ্বিতীয়টাই সম্ভবত ঘটেছিল, ধারণা হয়েছিল তদন্তকারীদের।
জিজ্ঞাসাবাদে অমরেন্দ্র-হত্যার পরিকল্পনা যা জানা গেল, তা ঘোর লজ্জায় ফেলে দেবে যে-কোনও রুদ্ধশ্বাস গোয়েন্দা কাহিনিকে। ভাবুন একবার, প্রায় এক শতক আগে স্থির মস্তিষ্কে এক বছর তিরিশের যুবক ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণ ঘটিয়ে ভাইকে খুনের প্ল্যান করছে! শরদিন্দুর উপন্যাসে সাইকেল থেকে নিক্ষিপ্ত গ্রামোফোন পিন বা শজারুর কাঁটা দিয়ে খুনের কাহিনি বহুপঠিত। বাস্তবের বিনয়েন্দ্রর কুকর্মের অভিনবত্ব তুলনায় ঢের বেশি কূটবুদ্ধির, সন্দেহ নেই কোনও।
সম্পত্তির ন্যায্য প্রাপ্য অমরেন্দ্র দাবি করার দিন থেকেই বিনয়েন্দ্র ঘুঁটি সাজাতে শুরু করেন ভাইকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার। নাকে আঁটা চশমার মাধ্যমে Tetanus সংক্রমণের চেষ্টা যখন ব্যর্থ হল, তখন আরও প্রাণঘাতী কিছুর সন্ধানে মনোযোগী হলেন বিনয়েন্দ্র। ষড়যন্ত্রের শরিক হলেন তারানাথ। যিনি আদপে ডাক্তারই নন (ভুয়ো ডাক্তার সে-যুগেও ছিল!)। কর্নওয়ালিস স্ট্রিটে ‘Calcutta Medical Supply Concern’ নামে এক ল্যাবরেটরিতে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে কাজ করতেন। সেই সুবাদে অসুখবিসুখ সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা হয়েছিল। তারানাথই বুদ্ধি দিলেন, ঘাতক হিসাবে প্লেগ অব্যর্থ।
কিন্তু ভাবলেই তো হল না, প্রয়োগের উপায়? তার চেয়েও জরুরি, প্লেগের bacilli পাওয়া যাবে কোথা থেকে? কে দেবে? বোম্বাইয়ের হফকিন ইনস্টিটিউটের গবেষণাগারের শরণাপন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত হল।
‘Haffkine Institute for Training, Research and Testing’ স্থাপিত হয়েছিল ১৮৯৯ সালে, বোম্বাইয়ের পারেল অঞ্চলে। প্রতিষ্ঠাতা Dr Waldemar Mordecal Haffkine শুরুতে নাম রেখেছিলেন ‘Plague Research Laboratory’। তারানাথ টেলিগ্রাম করে ইনস্টিটিউটে জানালেন, তাঁর ট্রপিক্যাল মেডিসিনে ডিপ্লোমা রয়েছে। ব্যাকটেরিয়া-বাহিত রোগ নিয়ে গবেষণা করছেন, plague bacilli প্রয়োজন। ইনস্টিটিউট উত্তরে জানাল, কলকাতার surgeon general –এর সুপারিশ পাঠালে বিবেচনা করে দেখা হবে আর্জি। কিন্তু কে দেবে অজ্ঞাতকুলশীল তারানাথকে ওই মহার্ঘ সুপারিশপত্র, আর কেনই বা দেবে?
তা হলে? ডা. শিবপদ ভট্টাচার্য ও ডা. দুর্গারতন ধরের সঙ্গে ফের যোগাযোগ করলেন বিনয়েন্দ্র-তারানাথ। যথেষ্ট অর্থের প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে দুই চিকিৎসকও যোগ দিলেন প্লেগ-পরিকল্পনায়। ডা. ভট্টাচার্য দীর্ঘ সুপারিশ পাঠালেন তারানাথের হয়ে। উত্তর এল নেতিবাচক।
বিনয়েন্দ্র তবু অদম্য, একাধিকবার বোম্বাই গেলেন। সরকারিভাবে সুবিধে করতে পারলেন না। মরিয়া চেষ্টায় ইনস্টিটিউটের দুই ডাক্তারকে বিপুল অঙ্কের টাকার প্রলোভন দেখালেন লাগাতার। বিলাসবহুল Sea View Hotel-এ ব্যবস্থা করলেন যথেচ্ছ বিনোদনের, দিনের পর দিন। দুই ডাক্তার প্রলোভনে নতিস্বীকার করলেন শেষমেশ, কিন্তু লিখিত প্রমাণ রাখলেন না। সম্পূর্ণ বেসরকারিভাবে বিনয়েন্দ্র-তারানাথের কাছে পৌঁছল ‘লাইভ প্লেগ কালচারের’ vial। সেটা ৭ জুলাই, ১৯৩৩। তারানাথকে সুযোগ করে দেওয়া হল বোম্বাইয়ের প্লেগ হসপিটালে ‘bacteriologist’ পরিচয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার। সাদা ইঁদুরের উপর ব্যাকটেরিয়া-বিষ প্রয়োগ করে নিশ্চিত হলেন তারানাথ।
এরপর যা ঘটেছিল, লিখেছি আগেই। কুড়ি বছরের যুবকের দেহে প্লেগ bacilli ঢুকিয়ে বিরলতম হত্যা। যা হইচই ফেলে দিয়েছিল আসমুদ্রহিমাচলে।
কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দফতর, দাবিই করা যাক, অসামান্য তদন্ত করেছিল। যা মুক্তকণ্ঠে তারিফ করেছিলেন জজসাহেব তাঁর রায়ে। তদন্তকারী অফিসার শুরুর দিকে ছিলেন সাব ইনস্পেকটর শরৎচন্দ্র মিত্র, পরে ইনস্পেকটর এম এল রহমান। আততায়ীকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ, অদূর বা সুদূর ভবিষ্যতে পাওয়ার সম্ভাবনাও প্রায় শূন্য। এমন অবস্থায় বাকি ষড়যন্ত্রকারীদের শাস্তিদান নিশ্চিত করতে ভরসা শুধু অকাট্য যুক্তিতে মোটিভকে প্রমাণ করা এবং পারিপার্শ্বিক প্রমাণের (circumstantial evidence) জালটি এমন ভাবে বোনা যাতে ঘটনাপরম্পরার গতিপথ (chain of events) দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। এ কাজ যে কী ভীষণ কষ্টসাধ্য, সে তদন্তকারী অফিসারই শুধু জানেন।
মোটিভের অংশটি অবশ্য সহজসাধ্যই ছিল। অমরেন্দ্রর মৃত্যুতে বিনয়েন্দ্র যে লাভবান হতেন, সেটা তো জলবৎ তরলং ছিল। পারিপার্শ্বিক প্রমাণ একত্রিত করার দুরূহ কাজটি সুসম্পন্ন করতে প্রাণপাত করেছিলেন কলকাতার গোয়েন্দারা। বিনয়েন্দ্রর বোম্বাইযাত্রার দিনপঞ্জি এবং হোটেলবাসের প্রতিটি নথি জোগাড়, রেজিস্টারের হস্তাক্ষরের সঙ্গে অভিযুক্তের হস্তাক্ষর মেলানো, হফকিন ইনস্টিটিউটে যাতায়াতের প্রমাণ সংগ্রহ, তারানাথের টেলিগ্রাম এবং ডা. ভট্টাচার্যের সুপারিশপত্র, যে দোকান থেকে ইঁদুর কেনা হয়েছিল সেটি খুঁজে বের করে মালিকের জবানবন্দি, যে ট্যাক্সিতে করে বোম্বাইয়ের প্লেগ হসপিটালে পৌঁছেছিলেন তারানাথ, সেটিকে খুঁজে বের করা, পুঙ্খানুপুঙ্খ এমন আরও যে কত, লিখলে তালিকা দীর্ঘতর হতে থাকবে। বোম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন দরাজ সাহায্যের, নিয়মিত কলকাতার নগরপালের সঙ্গে আলোচনা করতেন তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে।
বিচারপর্বে অঢেল অর্থব্যয় করবেন বিনয়েন্দ্র, প্রত্যাশিতই ছিল | লাভ হয়নি যদিও। নিম্ন আদালত ফাঁসির আদেশ দেয় বিনয়েন্দ্র ও তারানাথকে। মুক্তি দেওয়া হয় ডা. ধর এবং ডা. ভট্টাচার্যকে। উচ্চ আদালতে আপিল পেশ হয় যথানিয়মে। ফাঁসির আদেশ কমে সাজা হয় ‘কালাপানির’, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। বিচারক লেখেন রায়ে, “probably unique in the annals of crime।”
মামলার নথিপত্রে লিপিবদ্ধ রয়েছে খুনের প্রস্তুতিপর্বে তারানাথকে ষড়যন্ত্রী আশ্বাস বিনয়েন্দ্রর, কেউ জানবে না, কে পিন ফুটিয়েছিল। খুনিই না পেলে পুলিশ কাঁচকলা করবে! সহজ হিসেব।
সহজ? সহজ আর থাকল কই? প্রেক্ষিত আলাদা, ব্যঞ্জনাও বহুমাত্রিক। তবু, এ কাহিনির উপসংহারে শঙ্খ ঘোষের কবিতার লাইন ঝলকে ওঠে স্বতঃস্ফূর্ত—
“এ কথা খুব সহজ, কিন্তু কে না জানে
সহজ কথা ঠিক ততটা সহজ নয়।”
১.০২ মানুষ বড় শস্তা, কেটে, ছড়িয়ে দিলে পারতো
[বেলারানী হত্যামামলা
তদন্তকারী অফিসার সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ]
দৃশ্য-১
৩০ জানুয়ারি, ১৯৫৪, ভোর সোয়া পাঁচটা, বড়জোর সাড়ে পাঁচ।
ভোর হয়েছে, সকাল নয়। রাসবিহারী থেকে চেতলার দিকে যেতে ডানহাতে কালীঘাটের বাস্তুহারা বাজার। দোকানপাটের ঝাঁপ খুলতে খুলতে সে আরও অন্তত কয়েক ঘণ্টা। বাজারের সাফাইকর্মীদের বেশির ভাগই অবশ্য উঠে পড়েন দিনের আলো ফুটতে না ফুটতেই। বেলা একটু বাড়লেই মেলা লেগে যাবে লোকের। আগে থেকে সাফসুতরো করে না রাখলে পরে সামলে ওঠা দায়।
এমনই একজন কর্মীর প্রথম চোখে পড়ল কাগজের মোড়কগুলো। তিনটে পাশাপাশি। পড়ে রয়েছে কেওড়াতলা শ্মশানের কাছে একটি শৌচালয়ের পাশে। সে তো কত কিছুই এদিকে-ওদিকে পড়ে থাকে, কিন্তু এ তো অন্যরকম! প্রথম দর্শনেই আঁতকে ওঠার মতো। নারকেল দড়ি দিয়ে বাঁধা কাগজের মোড়কগুলোর একটার কিছু অংশ ছিঁড়ে গিয়েছে। শুকিয়ে যাওয়া রক্তের লালচে ছোপ কাগজে। ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে দুটো আঙুল। ডাক্তারবদ্যি হওয়ার প্রয়োজন নেই, এক ঝলকেই বোঝা যায়, আঙুল মনুষ্যদেহের।
আতঙ্কিত চিৎকার-চেঁচামেচিতে লোক জড়ো হল দ্রুত। খবর গেল টালিগঞ্জ থানায়। অফিসাররা এসে কৌতূহলী ভিড় সরালেন প্রথমে, খোলা হল মোড়ক। একের পর দুই, দুয়ের পর তিন। বেরোল দুটো হাতের টুকরো টুকরো খণ্ড। বাহুমূল থেকে কনুই। কনুই থেকে আঙুল। ছিন্নভিন্ন। কাগজের মোড়কটি দেখা হল খুঁটিয়ে। ২১ নভেম্বরের ‘যুগান্তর’।
দৃশ্য-২
৩০ জানুয়ারি, ১৯৫৪, ভরদুপুর।
সবে খেয়ে উঠেছেন কালীঘাট পার্কের বহুদিনের দারোয়ান। শীতের ঝিমধরা দুপুরে ইতস্তত ঘুরছেন গাছগাছালিতে ঘেরা উদ্যানের এদিক-সেদিক, রোজকার অভ্যাসমতো। ঘুরতে ঘুরতেই চোখ আটকে গেল একটা আমগাছের পিছনে। ঝোপঝাড়-আগাছার জঙ্গলে কী পড়ে আছে ওগুলো? চারটে কাগজের মোড়ক, বাঁধা ওই নারকেল দড়ি দিয়েই। কৌতূহলবশত খুলেই ফেললেন। ভিতরে যা দেখলেন, ঊর্ধ্বশ্বাস ছোটাছুটি করে এরপর শ’খানেক পথচলতি মানুষের ভিড় জুটিয়ে ফেলতে লাগল খুব বেশি হলে মিনিটদুয়েক।
একটি মোড়কে হাঁটু থেকে কাটা দুটি পায়ের অংশ। দ্বিতীয়টিতে নারীশরীরের উপরিভাগ ত্রিখণ্ডিত অবস্থায়। তিন নম্বর মোড়কে ধড় থেকে আলাদা করে দেওয়া মাথা। নাক-কান-ঠোঁট-চুল বিহীন। মুখের চামড়া চেঁছে তুলে নেওয়া হয়েছে। আঘাতের তীব্রতায় চূড়ান্ত বিকৃত করে দেওয়া হয়েছে মুখাবয়ব। কয়েকগাছি চুল, মাত্র কয়েকগাছিই, লেগে রয়েছে কপালের উপরে।
শেষ মোড়কটিতে মিলল একটি ভ্রূণ। যাতে চোখ বুলোলেই মালুম হয়, পৃথিবীর আলো দেখার আর বেশি দেরি ছিল না। মৃতা সন্তানসম্ভবা ছিলেন, প্রসবমুহূর্ত এসেই গিয়েছিল প্রায়।
ফের থানাপুলিশ। খবর পেয়েই টালিগঞ্জ থানার অফিসাররা ছুটলেন ঊর্ধ্বশ্বাসে, সকালের উদ্ধার হওয়া দেহাংশ নিয়ে ধন্দ তখনও কাটেনি। লালবাজার থেকেও হোমিসাইড বিভাগের গোয়েন্দাদের নিয়ে গাড়ি ছুটল। গন্তব্য, লেখা বাহুল্য, কালীঘাট পার্ক।
চারটি মোড়কই দেখা গেল ‘যুগান্তর’-এর। ২১ নভেম্বর, ১৯৫৩, ১০ জানুয়ারি, ১৯৫৪, ২৫ জানুয়ারি ও ২৬ জানুয়ারি, ১৯৫৪।
পার্কের চিরুনিতল্লাশিতে পাওয়া গেল আরও একটি মোড়ক। রাখা ছিল একটি বালির বস্তার নীচে। যার ভিতর থেকে বেরল দুই ঊরুর টুকরো টুকরো অংশ।
মোড়ার জন্য ব্যবহৃত কাগজ? সেই ‘যুগান্তর’-ই।
দৃশ্য-৩
২৭ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪, মধ্যরাত অতিক্রান্ত।
লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের ইন্টারোগেশন রুম। লাগাতার জেরায় ধুঁকছেন মধ্যতিরিশের যুবক। জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে সন্ধে নাগাদ, চলছে বিরামহীন। অবলীলায় সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন শুরুর কয়েক ঘণ্টায়। এমনটাই হয় জটিল মামলায়, জানি আমরা অভিজ্ঞতায়। জেরার প্রাথমিক পর্বে অভিযুক্ত কিছুতেই স্বীকার করে না অপরাধ। আত্মপক্ষ সমর্থনে যা বলার, যে ভাবে বলার, বলতে দেওয়া হয় সব। তদন্তকারীরা শুনতে থাকেন নিরাবেগ নিস্পৃহতায়, বক্তব্যের অসংগতি লিপিবদ্ধ হতে থাকে নীরবে।
একটা সময়ের পর, নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার আত্মতুষ্টি যখন অজান্তেই ঘিরে ধরে অভিযুক্তকে, আসল খেলা শুরু হয় ঠিক তখন। প্রশ্নের তাস একটার পর একটা ফেলতে থাকেন গোয়েন্দারা, চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হয় জবানবন্দির অসংগতি, যার ধাক্কায় বেআব্রু হয়ে যায় বয়ানের মিথ্যাচার।
তেমনটাই হল সে-রাতে। প্রশ্নের চক্রব্যূহে ক্রমশ দিকভ্রান্ত হতে থাকলেন যুবক। প্রথম দিকের ‘ভাঙব, তবু মচকাব না’ ভাবটা কমতে কমতে প্রায় শূন্যের কাছাকাছি তখন। স্নায়ু যে বিদ্রোহ করতে শুরু করেছে, জানান দিচ্ছে কপালের স্বেদবিন্দু। ভঙ্গুর হয়ে এসেছে রক্ষণ।
সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, তৎকালীন ওসি হোমিসাইড, বুঝলেন, কাঙ্ক্ষিত স্বীকারোক্তি আসা স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। এলও অল্পক্ষণ পরেই। ‘স্যার, আমিই মেরেছি ওকে। কেটে ফেলে দিয়েছি টুকরো টুকরো করে। এ ছাড়া উপায় ছিল না আর!’ বলেই মুখ ঢেকে টেবিলে মাথা গুঁজে দিলেন অভিযুক্ত।
সমরেন্দ্র জলের গ্লাস এগিয়ে দিলেন, ‘নিন, খান। অনেক সময় আছে। ধীরেসুস্থে বাকিটা বলুন।’ রাত তখন পাড়ি দিচ্ছে ভোরের ঠিকানায়। সূর্যের দাপট কিছু পরেই দখল নেবে অন্ধকারের।
বেলারানী দত্ত হত্যা মামলা। টালিগঞ্জ থানা, কেস নম্বর ১১৬, তারিখ ৩১/১/৫৪। খুন এবং প্রমাণ লোপাট, ৩০২/২০১ আইপিসি।
ছড়িয়ে-ছিটিয়ে নারীশরীরের দেহাংশ খবরের কাগজে মুড়ে, বিকৃত এতটাই যে শনাক্তকরণ প্রায় অসাধ্য। সাম্প্রতিক অতীতে এ ধরনের কিছু ঘটনা ঘটেছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। ইন্টারনেটের দৌলতে সেসব মামলার বিবরণও সহজলভ্য। চিত্রায়িতও হয়েছে সিরিয়ালে-সিনেমায়। কিন্তু সেই সদ্য স্বাধীনোত্তর সময়ে এমন কেস কলকাতায় কেন, দেশের অন্যত্র বা বিদেশেও আদৌ হয়েছিল কি না, তথ্য নেই প্রামাণ্য।
ঘটনা প্রচারিত হওয়ার পর শহর কলকাতায় প্রবল চাঞ্চল্য প্রত্যাশিতই ছিল। চাঞ্চল্যের অভিঘাত ক্ষীণতর হয়েছে সময়ের স্বাভাবিক নিয়মে, কিন্তু বিরলের মধ্যে বিরলতম হিসেবে এই মামলার চিরস্থায়ী স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে অপরাধ-গবেষণার ইতিহাসে।
নারকীয় হত্যাকাণ্ডের তদন্তভার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের হাতে তুলে দিতে বিন্দুমাত্র সময় খরচ করলেন না তৎকালীন নগরপাল। দায়িত্ব পড়ল হোমিসাইড শাখার ওসি ইনস্পেকটর সমরেন্দ্রনাথ ঘোষের উপর, আগে লিখেছি যাঁর কথা।
ময়নাতদন্ত হল ৩১ জানুয়ারি। পচনপ্রক্রিয়া ততক্ষণে শুরু হয়ে গিয়েছে দেহাংশে। খণ্ডিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের একটি একটি করে অশেষ অধ্যবসায়ে জোড়ার চেষ্টা করলেন ডাক্তাররা। সাত-আট ঘণ্টার প্রাণান্তকর পরিশ্রমে পূর্ণবয়স্কা নারীশরীরের রূপ নিল জোড়া লাগানো দেহাবশেষ। দুটি বিশেষত্ব নজরে এল মৃতদেহে। এক, দুটি পায়েরই পাতা অস্বাভাবিক লম্বা। দুই, বাঁ ঊরুর উপর একটি কাটা দাগ।
যিনি পোস্টমর্টেম করলেন, তাঁর বক্তব্য ছিল দ্বিধাহীন। মৃত্যু ঘাড়ের কাছে ধারালো কিছুর আঘাতে, যা “ante mortem and homicidal in nature”। শরীরের বাকি অগুনতি আঘাতচিহ্ন মৃত্যুর পর, “post mortem injuries”।
এ পর্যন্ত তো হল। কিন্তু আসল কাজই তখনও বাকি, মৃতার শনাক্তকরণ। মুখ ক্ষতবিক্ষত, চামড়া বলতে কিছু অবশিষ্ট নেই আর। কে খুন হলেন, সেটা না জানলে কীভাবে খুন, কে খুনি, এগোনোর রাস্তাই তো একপ্রকার বন্ধ হয়ে যায় তদন্তের।
শেষ চেষ্টা করা হল। খবর পাঠানো হল চুঁচুড়া-নিবাসী ডাক্তার মুরারীমোহন মুখার্জির কাছে। যিনি তখন কলকাতার কারনানি হাসপাতালে প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগের প্রধান, বিস্তর নামডাক।
ডাক্তার মুখার্জি এলেন, অক্লান্ত শ্রমব্যয় করলেন। মুখের আদল কিছুটা এল বটে, কিন্তু তা চিহ্নিতকরণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। পচনক্রিয়া (Putrefaction) শুরু হয়ে গিয়েছিল দেহাংশে। না হলে প্লাস্টিক সার্জারি ফলদায়ক হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা ছিল। ভারতের ইতিহাসে অপরাধ-তদন্তে সম্ভবত এই মামলাতেই প্রথম প্লাস্টিক সার্জারির শরণাপন্ন হওয়া।
কলকাতা পুলিশের তরফে ঘটনার বিশদ প্রচার করা হল। কাগজে মৃতার অবয়বের ছবিও ছাপানো হল, যা তোলা হয়েছিল ময়নাতদন্তের পর। দিন গড়িয়ে সপ্তাহ পেরোল, সামান্যতম খবরও এল না।
মর্গে খণ্ডিত দেহাংশ জোড়া হয়েছে
নীলরতন সরকার হাসপাতালের মর্গে দেহ রাখা হল প্রায় কুড়ি দিন। এর পর মৃতার কপালে আটকে থাকা কিছু চুল, হাতের-কোমরের-পায়ের-ঊরুর কিছু অস্থিমজ্জা সংরক্ষিত করে অশনাক্ত দেহ পুড়িয়ে ফেলা হল প্রথামাফিক।
শনাক্ত করার জন্য কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি রাখেনি পুলিশ। যেখানে দেহের টুকরোগুলি ফেলা হয়েছিল, তার আশেপাশের অন্তত শ’খানেক বাসিন্দাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। শুধু শহরে নয়, রাজ্যের প্রতিটি থানায় বিস্তারিত খোঁজ নেওয়া হয়েছিল। কোথাও কোনও মহিলার নামে মিসিং ডায়েরি হয়েছে কি না। সূত্র মেলেনি কোনও।
ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহ। প্রায় মাসখানেক গড়িয়ে গিয়েছে ঘটনার। তদন্তে কণামাত্র অগ্রগতি ব্যতিরেকেই। কিনারাসূত্র আপ্রাণ চেষ্টাতেও অধরা থাকলে শতকরা নব্বই ভাগ তদন্তকারীকে একটা সময় গ্রাস করেই অনিবার্য হতাশা। যা ক্রমাগত অবচেতনে বাজাতে থাকে কাটা রেকর্ড, ‘অনেক হল, এবার হাল ছেড়ে দেওয়া যাক, কত মামলারই তো কিনারা হয় না।’
এমতাবস্থায় হতাশাকে প্লেগবৎ পরিত্যজ্য রাখাটাই সফল তদন্তকারীর কষ্টিপাথর। সমরেন্দ্র হাল ছাড়ার পাত্র ছিলেন না। ফুটবলের তুলনা টানলে, ব্রাজিল বা আর্জেন্টিনা নয়, ছিলেন আদ্যন্ত জার্মান মনোভাবাপন্ন। হারার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত না হারায় বিশ্বাসী, শিল্পের থেকে বরাবর প্রাধান্য দিতেন শৌর্যকে।
কথায় বলে, ভাগ্য বীরেরই সহায় হয়। আর, তদন্তের অভিজ্ঞতা বলে, ভাগ্য সহায় হয় একমুখী অধ্যবসায়েরও। কৃপাদৃষ্টি দেয় আচম্বিতে, ঘটে যায় অভাবিত সমাপতন।
যেমনটা হল ২৫ ফেব্রুয়ারির রাতে। রাত সাড়ে ন’টা-পৌনে দশটা হবে তখন। কর্মব্যস্ত দিনের শেষে বাড়ি ফিরছিলেন সমরেন্দ্র। ক্লান্ত, অবসন্ন। ঠান্ডাও লেগেছে একটু, হালকা সর্দিকাশিতে বিব্রত। গাড়ি ছুটছে টালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে রাসবিহারীর দিকে। হঠাৎই খেয়াল হল, একটা কাশির ওষুধ কিনে নিয়ে গেলে মন্দ হয় না। রসা রোডের কাছাকাছি এসে চোখে পড়ল প্রায় পাশাপাশিই দুটো ওষুধের দোকান। একটার ঝাঁপ ফেলছে কর্মচারী, Royal Medical Store। পাশেরটা খোলা, South Calcutta Pharmacy। গাড়ি দাঁড়াল দোকানের সামনে।
দোকানের ছিরিছাঁদ দেখলে ভক্তি হওয়ার কথা নয়। টুলে বসে একজন কর্মচারী, অপরিচ্ছন্ন পোশাক। মুখে জন্মজন্মান্তরের বিরক্তি। দোকানের তাক-আলমারির সিংহভাগই খালি, কিছু ওষুধপত্র সাজানো অবিন্যস্ত। পুলিশের গাড়ি থেকে খদ্দের নামতে দেখে সামান্য নড়েচড়ে বসলেন কর্মচারী।
—কাশির ওষুধ লাগবে একটা।
—দাঁড়ান স্যার, দেখছি।
মিনিটখানেক দেখেশুনে কর্মচারী দেঁতো হেসে যে উত্তর দিলেন, একটু রেগেই গেলেন সমরেন্দ্র।
—স্যার, জ্বর-মাথাব্যথার আছে। কাশির ওষুধ ছিল, স্টক শেষ।
—তা এমন দোকান খুলে রেখেছ কেন? বন্ধ করে দিলেই হয়। মালিক কোথায় তোমার?
—মালিক তো স্যার মাসখানেক হল আসছেন না।
—সে জন্যই এই অবস্থা দোকানের। কী নাম মালিকের? দোকানটা তুলে দিতে বলে দিয়ো।
—স্যার, বীরেন দত্ত। খবর পাঠিয়েছেন, বাইরে আছেন। রোজ সন্ধেবেলা দোকানে বসতেন। এই প্রথম এতদিন ধরে দেখছি না।
পাওয়া গেল না ওষুধ, চালক স্টার্ট দিলেন গাড়িতে। সামান্য এগনোর পরই গাড়ি থামালেন সমরেন্দ্র। দোকানের কর্মচারী কী বলল যেন? মালিক মাসখানেক ধরে আসছেন না? আরও তো বলল, ‘এই প্রথম এত দিন ধরে…’। সমরেন্দ্র ‘যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই’-এর তত্ত্বে ভরসা রাখতেন। মনের খচখচানি দূর করতে চালককে বললেন, যা তো আবার, দোকানটার মালিকের ঠিকানা জেনে আয়।
জানা হল। ৫৫/৪/২ টার্ফ রোড। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের অদূরেই। শরীর বইছিল না, তবু মনে হল সমরেন্দ্রর, একবার ঘুরেই আসি। গেলেন, দেখলেন বীরেন দত্তর ঘর তালাবন্ধ। প্রতিবেশীদের থেকে জানলেন, গত বেশ কয়েক বছর ধরে ওই ঘরেই বীরেন থাকেন স্ত্রী বেলাকে নিয়ে। একটি ছ’ বছরের ছেলেও আছে। জানুয়ারির শেষে সন্তানসম্ভবা বেলা ভরতি হয়েছিলেন শিশুমঙ্গলে, এমনটাই তাঁরা শুনেছিলেন বীরেনের কাছে। ৩০ জানুয়ারির পর বীরেনকে তাঁরা আর দেখেননি, ছেলেকে নিয়ে চলে গিয়েছেন।
কিনারার সম্ভাবনার ইঙ্গিত পেলে যে-কোনও তদন্তকারী অফিসারের যা হয়, তা-ই হল সমরেন্দ্রর। অ্যাড্রিনালিনের বাড়তি ক্ষরণ শিরা-উপশিরায়। এ অনুভূতি বড় পরিচিত পুলিশের, যাঁরা জটিল মামলার তদন্ত করেছেন, তাঁরা জানেন। লিখে বোঝানোর নয় সবটা।
বেলা দত্ত নামে কোনও সন্তানসম্ভবা যে গত এক মাসে ‘শিশুমঙ্গল’ হাসপাতালে ভরতি হননি, সেটা বার করতে লাগল ঘণ্টাদুয়েক। রহস্য আর পরদানশিন থাকল না |
আক্ষরিক অর্থেই ঝাঁপিয়ে পড়লেন হোমিসাইড বিভাগের গোয়েন্দারা। একটি লোককে খুঁজে বার করতে হবে। নাম জানা আছে। জানা হয়ে গিয়েছে কোথায় কীসের দোকান, বাড়ির ঠিকানা পাওয়া গিয়েছে। প্রতিবেশীরা চেহারার বিবরণ দিয়েছেন। এর পরও সন্দেহভাজনকে পাওয়া যাবে না, হয়? সোর্স লাগানো হল একাধিক। বীরেন দত্তর পারিবারিক এবং ব্যবসায়িক ঠিকুজিকুষ্ঠির খোঁজখবর শুরু করার চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই খবর এল। বীরেনের নাকি হরিশ মুখার্জি রোডেও আস্তানা আছে একটা, যাতায়াত নিয়মিত।
নজরদারি চালু হল। ২৭ ফেব্রুয়ারির ভোরে ১০২এ হরিশ মুখার্জি রোডের একটি বাড়ি থেকে চাদর মুড়ি দিয়ে এক ভদ্রলোককে বেরতে দেখা গেল। কেদার বোস লেনের মুখে আটকাল সাদা পোশাকের পুলিশ।
—আপনি কি বীরেন দত্ত?
—হ্যাঁ, কেন?
—বেলা দত্ত কি আপনার স্ত্রী?
—হ্যাঁ… কিন্তু…কেন বলুন তো?
—যা জানতে চাইছি, উত্তর দিন। উনি কোথায়?
—লজ্জার কথা কী আর বলব! বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে প্রেমিকের সঙ্গে।
—গাড়িতে উঠুন, আমরা লালবাজার থেকে আসছি। বাকি কথা ওখানেই হবে।
খুনের গায়ে-কাঁটা-দেওয়া বিবরণে আসার আগে একটু পূর্বকথন জরুরি। বীরেন দত্ত, ডাকনাম বেচু, বয়স ৩৪। বজবজের কাছের একটি গ্রামে কেটেছিল ছেলেবেলা। বাবা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সাব-ইনস্পেকটর। বয়স যখন মাত্র এক, বাবা গত হলেন। তার কয়েক মাসের মধ্যে মা-ও। দুই দিদি, আভা ও কনক। যাঁদের শ্বশুরবাড়ি যথাক্রমে আন্দুল ও কলকাতায়। বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর কিছুদিন থাকলেন দিদার গ্রামের বাড়িতে। ভরতি হলেন স্কুলে।
বীরেনের দুই খুড়তুতো দাদা নবনী দত্ত ও যতীন্দ্র দত্ত থাকতেন ভবানীপুরের চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে। বয়স যখন আট-নয়, দাদারা বীরেনকে নিয়ে এলেন কলকাতায় নিজেদের কাছে। বালক বীরেনকে ভরতি করে দেওয়া হল রামরিক ইনস্টিটিউশনে।
পড়াশোনায় যে বিশেষ মন ছিল বীরেনের, এমন অভিযোগ অতি বড় শুভানুধ্যায়ীর পক্ষেও করা কঠিন ছিল। রেজাল্ট তো খারাপ হচ্ছিলই, উপরন্তু ক্লাস পালিয়ে প্রাপ্তবয়স্কদের সিনেমা, বিড়ি-সিগারেট-মদ। উচ্ছন্নে যাওয়ার ইঙ্গিত ক্রমশ স্পষ্টতর হচ্ছিল। দাদারা একদিন বকাবকি করলেন খুব, চড়-থাপ্পড় খরচ করলেন দরাজহস্তে। ক্লাস এইটের বীরেন রেগেমেগে চলে এলেন আন্দুলে দিদির শ্বশুরবাড়িতে।
বেলারানী দেবী
জামাইবাবুর ওষুধের দোকান ছিল, টুকটাক কাজ শুরু করলেন সেখানে। ১৯৩৪ থেকে ’৪৪, দশ বছর কাটল আন্দুলেই। খুড়তুতো দাদা নবনীর বরাবরই কিঞ্চিৎ দুর্বলতা ছিল ‘বেচু’র প্রতি। নিয়মিত খবর রাখতেন। আন্দুলে গেলেন একদিন খোঁজখবর নিতে, যেমন যেতেন মাঝেমধ্যে। বীরেনকে একটু ছন্নছাড়া দেখলেন, মায়াই হল একরকম। ফের নিয়ে এলেন কলকাতায়। বীরেন তখন বছর চব্বিশের যুবক। বড় জামাইবাবু শ্যালককে ভালবাসতেন খুব। রসা রোডে ‘South Calcutta Pharmacy’ নামে একটি দোকান করেছিলেন কিছুদিন আগে। সেটা লিখে দিলেন বীরেনের নামে।
দাদা নবনীর রমেশ মিত্র রোডের বাড়িতে বসবাস শুরু করলেন বীরেন। নবনীর কন্যা কমলা তখন সতেরোর কিশোরী। ছটফটে, হাসিখুশি, প্রাণবন্ত। খুড়তুতো দাদার মেয়ের প্রেমে পড়লেন বীরেন। কমলাও ভেসে গেলেন কৈশোরের আবেগে। অনুরাগ ছিল উভয় পক্ষেই।
কমলাকে নিয়ে একদিন বাড়ি থেকে পালালেন বীরেন, উঠলেন সদানন্দ রোডের এক ভাড়াবাড়িতে। চেষ্টাও করলেন বারদুয়েক নবনীর বাড়ি গিয়ে বোঝাতে, ফল হল না। তুমুল বাদানুবাদ হল। নবনীর পরিবার এই সম্পর্ককে মানলেন না কিছুতেই। মেয়েরও এই গৃহত্যাগে সম্মতি আছে বুঝে নবনী সম্পর্ক ত্যাগ করলেন কমলার সঙ্গে। পুলিশে অভিযোগ করবেন ভেবেছিলেন প্রথমে। শেষমেশ অবশ্য বিরত থাকলেন সামাজিক মর্যাদাহানির আশঙ্কায়।
সদানন্দ রোডের বাড়িতে সংসার পাতলেন বীরেন, নতুন নামও দিলেন কমলার। ‘বেলারানী’। আইনসিদ্ধ বিয়ের প্রথাগত রীতিনীতি অবশ্য মানলেন না বীরেন, বেলার শত অনুরোধ সত্ত্বেও। সিঁথিতে নাম-কা-ওয়াস্তে সিঁদুর ঠেকিয়ে নিরস্ত করলেন বেলাকে, স্বামী-স্ত্রী পরিচয়েই দিন কাটতে লাগল। পুত্রসন্তানের জন্ম হল বছরদুয়েকের মধ্যে। নাম রাখা হল বথীন্দ্রনাথ দত্ত, আদরের ডাক ‘বোতন’।
সন্তানের জন্মের পর বীরেন-বেলা সদানন্দ রোডের বাড়ি থেকে উঠে এলেন ৫৫/৪/২, টার্ফ রোডে। যত সময় গেল, বীরেন ক্রমে বেলার প্রতি নিরুৎসাহ হয়ে পড়তে লাগলেন। আলাপ হল শ্রীকৃষ্ণ লেনের বাসিন্দা শ্রী সরোজকান্তি বসুর কন্যা মীরার সঙ্গে। ’৪৮-এর মাঝামাঝি রেজিস্ট্রি বিয়ে সেরে ফেললেন। বেলার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ গোপন করেই। বীরেনের দিদি-জামাইবাবুরা জানতেন বেলা-কাহিনি, কিন্তু তাঁরাও তীব্র বীতশ্রদ্ধ ছিলেন ওই সম্পর্ক নিয়ে। ভাবলেন, বেলা তো এক অর্থে রক্ষিতাই মাত্র, বিয়ে হলে যদি সম্পর্কে ইতি পড়ে, ভালই। এতে যে কারওরই ভাল হবে না, বেলারই হোক বা মীরার, বা বীরেনেরও, সেটা বিলক্ষণ বুঝেও। ওই যে, স্নেহ বড় বিষম বস্তু!
বিয়ের পরে প্রথম দু’বছর গোয়াবাগানে দিদির শ্বশুরবাড়িতে মীরাকে রাখলেন বীরেন। সেখানেই জন্ম হল এক কন্যাসন্তানের, যে পৃথিবীর মায়া কাটাল ভূমিষ্ঠ হওয়ার দু’দিন পরেই। মীরা সদ্যোজাতা কন্যার মৃত্যুশোকে আচ্ছন্ন ছিলেন কিছুদিন। শোকের প্রাবল্য কিছুটা কমলে বীরেনকে বললেন, বাড়ি খুঁজতে শুরু করো, আলাদা থাকব। বাস্তবিকই, কোন বিবাহিতা মহিলাই বা চান ওভাবে থাকতে ননদের অনুগ্রহে?
নাছোড়বান্দা মীরার জোরাজুরিতে বীরেন ১০২এ হরিশ মুখার্জি রোডের একতলার একটি ছোট ঘর ভাড়া নিলেন। ১৯৫৩-য় জন্ম নিল বীরেন-মীরার শিশুপুত্র।
আশ্চর্য কৌশলী রোজনামচা ছিল বীরেনের! কতই বা দূরত্ব টার্ফ রোড আর হরিশ মুখার্জি রোডের? অথচ, বছরের পর বছর মীরাকে জানতে দেননি বেলার কথা, বেলাকে মীরার! দুপুরের খাওয়া সারতেন টার্ফ রোডে, মীরাকে বলতেন, কাজের ব্যস্ততায় মধ্যাহ্নভোজ সেরে নিতে হয় ওয়াইএমসিএ–র ক্যান্টিনে। রাতটা সপ্তাহের অধিকাংশ দিন কাটাতেন হরিশ মুখার্জি রোডের ভাড়াবাড়িতে। বেলাকে বুঝিয়েছিলেন, দোকানের ওষুধপত্র কেনার কাজে শহরের বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন পড়ে ঘনঘন।
বিবেকবর্জিত দুশ্চরিত্র ছিলেন বীরেন, ঠিকই। কিন্তু সত্যের স্বার্থে স্বীকার্য, গুণও ছিল কিছু। ছোট থেকেই পাড়ায় যাত্রা-নাটকে অভিনয় করতেন এবং নেহাত মন্দ করতেন না। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিয়োয় যাতায়াত ছিল নিয়মিত। সেখানেই আলাপ-পরিচয় প্রযোজক-পরিচালকদের সঙ্গে। একটা-দুটো নয়, অভিনয় করেছিলেন ছ’টি ছবিতে। যার মধ্যে বাঙালির সর্বকালীন মহানায়কের কেরিয়ারের দ্বিতীয় মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি ‘কামনা’-ও ছিল। বাকি ছবিগুলি ‘নারী’, ‘মহাকাল’, ‘শুভদা’, ‘নিষ্কৃতি’ এবং ‘পাপের পথে’।
‘পাপের পথে’ আক্ষরিক অর্থেই পা বাড়ানো অবশ্য ওই স্টুডিয়োপাড়া থেকেই। জুটে গেল কিছু ইয়ারদোস্ত। রেসের মাঠ, জুয়ার ঠেক আর নিষিদ্ধ পল্লির ত্র্যহস্পর্শে দিশা হারালেন। ফার্মাসির কাজকর্মে মন দিতেন না আর। কর্মচারীদের উপর ছেড়ে দিলেন পুরোটাই। ফল, বাণিজ্যলক্ষ্মী বিরূপ হলেন, শুরু হল অর্থসংকট। এমনিতেই দুটো সংসার চালানো যথেষ্ট ব্যয়সাপেক্ষ ছিল। কষ্টেসৃষ্টে তবু চলছিল। কিন্তু বীরেন চোখে অন্ধকার দেখলেন, যখন জানলেন, বেলা দ্বিতীয়বারের জন্য সন্তানসম্ভবা।
—এর পর?
—আমি আর পারছিলাম না স্যার। একে ব্যবসায় মন্দা চলছে। অনেক ধারদেনা হয়ে গিয়েছিল। তার উপর বেলা আর মীরাকে মিথ্যে বলে বলে ক্লান্ত। ভয় হত স্যার, যে-কোনও দিন ধরা পড়ে যাব। মীরা তো সন্দেহ করতে শুরু করেইছিল, বেলাও মাঝেমধ্যেই জিজ্ঞেস করত, রোজ রাত্রে কীসের এত কাজ? যখন শুনলাম, বেলা আবার মা হতে চলেছে, প্রথমেই মাথায় এল, আবার একগাদা খরচের ধাক্কা। ঠিক করলাম, বেলাকে সরিয়ে দেব। আর কোনও উপায় ছিল না স্যার, বিশ্বাস করুন!
বিশ্বাস-অবিশ্বাস পরে। জিজ্ঞাসাবাদের গোড়ার কথা, খুব বেশি বিরাম দিতে নেই স্বীকারোক্তির সময়। গোয়েন্দারা থামতে দিলেনও না। বীরেন বলে চললেন।
—এক চোট রাগারাগি করলাম প্রথমে। বললাম, এ সন্তান আমার নয়, হতে পারে না। আমার রাতে বাইরে থাকার সুযোগ নিয়েছ তুমি। শুনে বেলা প্রথমে কাঁদল, তারপর ঝগড়াঝাঁটি হল খুব।
খুনের পরিকল্পনায় একমাত্র পথের কাঁটা ছিল পুত্র বোতন, বয়স তখন ছয়। কী করা যায়? মীরার কাছে আষাঢ়ে গপ্পো ফাঁদলেন বীরেন। বললেন, এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু আর তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছেন পথদুর্ঘটনায়। রেখে গিয়েছেন ছ’বছরের ছেলেকে, যে এখন সর্বার্থেই অনাথ। মীরা রাজি থাকলে হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে রাখতে চান। মীরা আবেগপ্রবণ স্বভাবের ছিলেন, সম্মতি দিলেন এক কথায়।
২৭ জানুয়ারি, ১৯৫৪। বেলা তখন পূর্ণ সন্তানসম্ভবা। ফার্মাসি থেকে বাড়ি ফিরলেন বীরেন। রাত প্রায় সাড়ে দশটা। বোতন ঘুমোচ্ছে অকাতরে। বেলা রুটি-আলুভাজা সাজিয়ে দিলেন থালায়। বীরেন নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করলেন। এবং করেই গালিগালাজ শুরু করলেন বেলাকে, আমি এক পয়সাও খরচ সেই বাচ্চার জন্য করব না, যে আমার নয়। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল বেলার, মেজাজ হারালেন, তোমার কীর্তিকলাপ জানতেও আর বাকি নেই কারও।
বীরেন সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিলেন। বেমক্কা মারধর শুরু করলেন। রান্নাঘরে রাখা দা দিয়ে বেলার ঘাড়ে কোপ বসালেন। বেশ কয়েকবার। অবিরাম রক্তক্ষরণ এবং মৃত্যু কিছুক্ষণের মধ্যেই। কাঠের আলমারিতে কাপড়চোপড় ছিল। সেসব বার করে আলমারিতেই ঢুকিয়ে দিলেন মৃতদেহ। ধুয়েমুছে পরিষ্কার করলেন রক্তস্রোত। তার আগে বেলার শরীরে যা গয়নাগাটি ছিল, খুলে নিলেন সব। ছ’জোড়া সোনার চুড়ি, সোনার আংটি, কানের দুল, সব। এবং, এত কিছুর পর, ঘুমিয়ে পড়লেন নিশ্চিন্তে!
খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র
উদ্ধার করা বেলারানীর বালা
টার্ফ রোডের বাড়ির দু’তলায় একাই থাকতেন বেণু নামের এক অবিবাহিতা মহিলা। যাঁর সঙ্গে বেলার ঘনিষ্ঠতা ছিল, যিনি অসম্ভব ভালবাসতেন বোতনকে। বোতন দিনের অনেকটা সময় কাটাত ‘বেণুমাসি’র সঙ্গে। ২৮ তারিখ ভোরে উঠেই পরের ধাপগুলো ছকে নিলেন বীরেন। কীরকম?
—ভোরে উঠে বেণুদিকে ডাকলাম। বললাম, গভীর রাতে বেলাকে ভরতি করাতে হয়েছে শিশুমঙ্গল হাসপাতালে। ডেলিভারি হবে যে-কোনও সময়। বোতনকে এ ক’দিন যদি বেণুদি নিজের কাছে রাখেন, ভাল হয়। বেণুদি সানন্দে রাজি হলেন। বোতন সকালে উঠে জানতে চাইল, মা কোথায়? বললাম, মা হাসপাতালে গিয়েছে, তোমার একটা ভাই বা বোন নিয়ে কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরে আসবে।
অচিন্তনীয়! বেলার লাশকে আলমারিবন্দি রেখে দিব্যি সকালে দোকানে বেরলেন বীরেন। ভাবতে থাকলেন সারাদিন, লাশ হাপিস করা যায় কীভাবে? লাশই যদি না পায় পুলিশ, কাকেই বা ধরবে, কীভাবেই বা ধরবে? রাত সাড়ে ন’টা নাগাদ কর্মচারীরা বেরিয়ে গেল, দোকানে জমিয়ে রাখা ‘যুগান্তর’-এর স্তূপ থেকে কয়েকটা বার করে নিলেন বীরেন। রওনা দিলেন টার্ফ রোড। পরের অংশ বীরেনের বয়ানেই পড়ুন, নিস্পৃহ বিবরণ দুঃসাধ্য।
—বেলার বডি বার করলাম আলমারি থেকে। প্রথমে দা দিয়ে মাথাটা কাটলাম। তারপর এক এক করে কান-নাক-চুল-হাত-পা-বুক-পেট, সব। মুখের চামড়া চেঁছে দিলাম। যুগান্তরের পাতা দিয়ে মুড়ে নারকেল দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখে দিলাম আলমারিতে। তালাও লাগিয়ে দিলাম। পুরো ঘরটা দু’-তিনবার ধুলাম ফিনাইল দিয়ে। রক্তে থইথই করছিল তো, গন্ধও বেরচ্ছিল খুব।
যে ঘরে বেলারানীকে হত্যা করা হয়েছিল
সে-রাতেও নিশ্চিন্ত নিদ্রা ওই ঘরেই!
২৯ তারিখ যথারীতি দিনভর ফার্মাসিতে। রাত্রে ফিরে বীরেন আলমারি খুলে বার করলেন নারকেল দড়ি দিয়ে বাঁধা মোড়কগুলো। রেশন আনার জন্য ব্যবহৃত দুটো বড় ব্যাগে বেলার খণ্ডিত দেহাংশ পুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে রিকশা ডাকলেন। কালীঘাট পার্কের কাছে গিয়ে ছেড়ে দিলেন রিকশা। কিছু মোড়ক ফেললেন পার্কে, কিছু হেঁটে বাড়ি ফেরার পথে কেওড়াতলা শ্মশানের কাছের শৌচালয়ের পাশে। টার্ফ রোডে ফিরে ফের একপ্রস্থ ধোয়ামোছা ফিনাইল দিয়ে, আলমারিতে বালতি বালতি জল ঢেলে মুছে ফেলা রক্তের দাগ।
৩০ জানুয়ারির সকাল। দোকানে বেরনোর সময় বীরেনের দেখা বেণুর সঙ্গে।
—বেলার কী খবর বীরেন? ভাবছিলাম, দেখতে যাব একবার।
—না না বেণুদি, এখন যেয়ো না। আজ রাতে ডেলিভারি হবে হয়তো। প্রেশারটা ওঠানামা করছে। ডাক্তাররা আলাদা কেবিনে রেখেছে। বাড়ি আসবে কয়েকদিনের মধ্যে, তখন তো দেখা হবেই।
উৎসুক প্রতিবেশীদেরও একই কথা বললেন। এবং পরের কয়েকদিন বেলার সমস্ত গয়নাগাটি সরিয়ে ফেললেন হরিশ মুখার্জি রোডে। মীরা জানতে চাওয়ায় বললেন, এক বন্ধু গয়না বন্ধক রেখেছেন। বেলার ব্যবহৃত কাপড়চোপড়–প্রসাধনী ফেলে দিলেন টালি নালায়। বোতনকে দিন দুয়েক পরে নিয়ে গেলেন হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে। অনাথ বন্ধুপুত্রের গল্প তো মীরাকে বলা ছিল আগেই। মীরা, অনুমান করা যায়, নির্ঘাত সন্দেহ করেছিলেন কিছু। বোতন নিশ্চয়ই মীরার সামনে ‘বাবা’ বলেই ডাকত বীরেনকে। ছ’বছরে অনাথ হওয়া বালক চট করে অন্য কাউকে ‘বাবা’ ডাকবে কেন? স্বামীর অপকীর্তি অনুমান করেও মীরা নীরব থেকেছিলেন, সংসাররক্ষার দায়ে?
সাক্ষ্যপ্রমাণ সংহত করা হল নিবিড় যত্নে। পান থেকে চুন খসারও বিলাসিতা ছিল না তদন্তকারী অফিসারের কাছে। হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়ি থেকে বাজেয়াপ্ত হল বেলার গয়না| টার্ফ রোডের বাড়ির আলমারি থেকে উদ্ধার হল দা (weapon of offence), যাতে লেগে ছিল চুল। মেঝেতে জমাট বেঁধে থাকা রক্তের দাগ থেকে সংগৃহিত হল নমুনা (sample blood)। উদ্ধার হল ফিনাইলের বোতল, যাতেও আটকে ছিল চুল। রক্তের নমুনা যে মনুষ্যদেহেরই, প্রমাণ হল ফরেনসিক পরীক্ষায়। মৃতা নারীর সংরক্ষিত চুল আর দত্তদের বাড়িতে দা আর ফিনাইলের বোতলে আটকে থাকা চুল যে একই ব্যক্তির, তা-ও নিশ্চিত হল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায়। এটি অত্যন্ত গুরুত্ত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল আদালতের বিচারে।
মৃতা যে বেলারানীই, প্রমাণের জন্য বেলার সন্তানসম্ভবা থাকার নথি একান্ত প্রয়োজন ছিল। সেটিও জোগাড় হল। টার্ফ রোডের বাড়ি তল্লাশির সময়ই পাওয়া গিয়েছিল শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের আউটডোরের টিকিট। ১৯৫৩-র ২৪ নভেম্বরের সেই টিকিটে স্পষ্ট লেখা ছিল, স্ত্রীরোগবিশারদের কাছে গিয়েছিলেন বেলা অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায়।
নিজের ফার্মাসিতে ‘যুগান্তর’ পত্রিকা রাখতেন বীরেন। বিক্রি করতেন না, পুরনো কাগজও জমিয়ে রাখার অভ্যাস ছিল। বাজেয়াপ্ত করা হল সমস্ত কাগজ। এবং ঠিক যেমনটা ভাবা হয়েছিল, সব ছিল কালানুক্রমিক, শুধু কয়েকটি দিন বাদে। সেই দিনগুলি, যে যে দিনের কাগজ দিয়ে মোড়া হয়েছিল বেলারানীর দেহের টুকরো টুকরো অংশ। পারিপার্শ্বিক প্রমাণ হিসেবে এর তাৎপর্য ছিল অপরিসীম, মাননীয় আদালতও লিপিবদ্ধ রেখেছিলেন রায়ে।
কালীঘাট পার্কে প্রাপ্ত পা-এর খণ্ডিত অংশ
ময়নাতদন্তের সময় আবিষ্কৃত মৃতার পায়ের পাতার অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্যের কথা উল্লেখ করেছি আগে। বীরেনের গ্রেফতারির পর খবর দেওয়া হল বেলারানীর আত্মীয়-পরিজনদের। যাঁদের সঙ্গে বীরেন-বেলার বিশেষ সম্পর্ক ছিল না পারস্পরিক তিক্ততার কারণে। মৃত্যুর খবরে ছুটে এলেন স্বজনরা। এবং দেখা গেল, বেলার বাবা-কাকা-ভাই-বোনের পায়ের পাতাও মৃতার মতোই একটু বেশি বড়।
ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের তৎকালীন ডেপুটি কমিশনার (ডিসি, ডিডি) চিঠি লিখলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের প্রথিতযশা অধ্যাপক ড. এস এস সরকারকে। মৃতার পায়ের পাতার ছবি এবং বাবা-কাকাদের পায়ের পাতার ছবি ট্রেসিং (tracing) করে পাঠালেন, জানতে চাওয়া হল, Anthropology-র তত্ত্ববিচারে কি বলা সম্ভব, এঁরা একই বংশোদ্ভূত কি না? গভীর পর্যবেক্ষণের পর ড. সরকার লিখিত মতামত পাঠালেন ইতিবাচক। হ্যাঁ, একই বংশের। প্রমাণের বুনিয়াদ দৃঢ়তর হল।
এত কাঠখড় পোড়ানোর প্রয়োজনই হত না আজকের দিন হলে, DNA পরীক্ষার সুবিধা থাকলে। কিন্তু তখনকার দিনে কোথায় সে সুবিধা? অপরাধ-তদন্তে DNA পরীক্ষার ব্যবহার তো শুরুই হয়েছে মাত্র কয়েক দশক আগে। ১৯৮৬ সালে ইংল্যান্ডের Leicester-এ দুটি খুন ও ধর্ষণের মামলায়।
বীরেনের কুকর্মের কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতা হল কমলা ওরফে বেলারানীর মায়ের সাক্ষ্যে। স্মরণ করুন, সংরক্ষিত ছিল মৃতার ঊরুর অংশবিশেষ। বাঁ ঊরুতে ছিল কাটা দাগ। যা এক ঝলক দেখেই আকুল কান্নায় ভাসলেন কমলা ওরফে বেলার গর্ভধারিণী। বললেন, আট বছর বয়সে পড়ে গিয়ে ঊরুতে গুরুতর চোট পেয়েছিল মেয়ে। এ দাগ সেই দাগ। মা তো, সন্তানকে কে আর তাঁর চেয়ে বেশি চিনবেন?
পেশ করা হল, এতটুকু অতিশয়োক্তি না করেই লিখছি, ‘সোনায় বাঁধানো’ চার্জশিট। যা খুনের মামলার তদন্তকারীদের কাছে আজও শিক্ষণীয় গ্রাহ্য হয়। আলিপুর দায়রা আদালতের বিচারপর্বে অভিযুক্তের আইনজীবী তর্কের তুফান তুললেন। দাবি, মৃতা আদৌ বেলারানী নন। বেলা অজ্ঞাতপরিচয় প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছেন। যে দাবি সর্বৈব মিথ্যায় পর্যবসিত হল ছ’ মাস ধরে চলা সওয়াল-জবাবের চাপানউতোরে। পারিপার্শ্বিক প্রমাণের নিশ্ছিদ্র বুনন এবং ফরেনসিক পরীক্ষার তথ্যের চুলচেরা বিশ্লেষণের পর বীরেনকে ফাঁসির সাজা শোনাল আদালত।
তদন্তকারী অফিসারের চিঠি
রায়ে পরিবর্তন হল না হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টেও। প্রাণদণ্ড বহাল থাকল। ১৯৫৬-র ২৮ জানুয়ারির ভোরে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসিকাঠ দেখা দিল নারকীয় অপরাধের কর্মফল রূপে। কালো কাপড়ে ঢাকল মুখ, গলায় আঁট হয়ে বসল দড়ি, পূর্বনির্দিষ্ট সময়ে বীরেন দত্তের পায়ের তলা থেকে সরে গেল পাটাতন।
Criminology বা অপরাধবিজ্ঞানের জনক বলা হয় ইতালীয় সমাজতাত্ত্বিক Cesare Lombroso (১৮৩৫-১৯০৯)-কে। যিনি বিজ্ঞান এবং নৃতত্ত্বকে এক যোগসূত্রে বেঁধে তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণে অপরাধীর মনের গহনতম অন্দরে ঢোকার প্রয়াস শুরু করেছিলেন। মূলত সেই আধারেই ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে এই বর্তমান সময় পর্যন্ত নিরন্তর জারি রয়েছে অপরাধ-গবেষণা। নিত্যনতুন বিশ্লেষণে অজানা দিগন্তের সন্ধান মিলছে প্রতিনিয়ত।
বেলারানী হত্যা মামলার তত্ত্বতালাশে কেস ডায়েরির হলুদ হয়ে আসা পাতা উলটোতে বসে তবু মনে হয়, কিছু ঘটনা থাকেই, যা গবেষণালব্ধ তথ্যের আজ্ঞাবহ নয়, যা জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যার অতীত। পড়লেন তো। ভাবুন, কোন তত্ত্বের ব্যাখ্যায় ধরা যায় বীরেন দত্ত রচিত নিধননাট্য, সে-যুগে যা পাশবিকতায় কল্পনাতীত এবং নৃশংসতায় নজিরবিহীন?
ত্রিনিদাদের বিশ্ববন্দিত ইতিহাসবিদ C .L. R. James (১৯০১- ৮৯) তাঁর বহুপঠিত বই ‘Beyond a boundary’ (১৯৬৩)-তে লিখেছিলেন, “What do they know of cricket who only cricket know?” যাঁরা শুধু ক্রিকেটই জানেন, তাঁরা আর কতটুকুই বা ক্রিকেট জানেন?
অপরাধীর মনের অন্দরমহলও তা-ই। যতটুকু দেখা যায়, জানা যায়, অদেখা-অজানা থেকে যায় ঢের বেশি। এ এক অন্য পৃথিবী। অন্য ছায়াপথ। যেখানে মনোজগতের আলো-আঁধারি ধোঁয়াশা-কুয়াশা এক বিছানায় শুয়ে থাকে পাশাপাশি।
যেভাবে রচিত হয়েছিল চিন্তাতীত হত্যালীলা, মনে পড়ে যায় কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সেই অমর লাইনদুটি। ব্যঞ্জনা বিস্তৃত বহুদূর, তা ছুঁতে চাওয়ার ধৃষ্টতা নেই। তবু, এ মামলার দলিল-দস্তাবেজ নাড়াচাড়ার সময় কী অমোঘ মনে হয় কবির ওই উচ্চারণ—
“পথের হদিশ পথই জানে, মনের কথা মত্ত
মানুষ বড় শস্তা, কেটে, ছড়িয়ে দিলে পারতো।”
১.০৩ অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো
[পঞ্চম শুক্লা হত্যামামলা
তদন্তকারী অফিসার অনিল ব্যানার্জি]
—রাগের মাথায় করে ফেলেছি স্যার, মাথার ঠিক ছিল না।
—ওটা ধরা পড়ার পর সবাই বলে।
—না স্যার, বিশ্বাস করুন…
—বিশ্বাস-অবিশ্বাস পরে। আগে বল, বডি কোথায়? তাড়াতাড়ি, বেশি সময় নেই হাতে।
—পুঁতে দিয়েছি স্যার।
—কোথায়?
—ঝিলে, কাদার তলায়।
—কোন ঝিল, কোথাকার? পুরোটা বল, না হলে বলানোর হাজারটা উপায় জানা আছে আমাদের।
—বলছি স্যার। তারাতলার কাছে।
—গাড়িতে ওঠ।
আদেশ নির্বিবাদে পালন করেন মধ্যতিরিশের বিহারি যুবক। বন্দর অঞ্চল থেকে গাড়ি যাত্রা শুরু করে গন্তব্যে, তারাতলা।
—ঝিলটা কোথায়?
—বাঁ দিকের রাস্তাটায় ঢুকতে হবে স্যার …
গাড়ি থামল তারাতলা রোড থেকে একটু ভিতরে একটি ঝিলের সংলগ্ন এলাকায়। মধ্যরাত অতিক্রান্ত তখন। রাস্তাঘাট জনমানবহীন, যথেষ্ট আলোকিত নয়। পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন জেরায় বিধ্বস্ত যুবক, টর্চ হাতে অনুসরণে কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের অফিসাররা। অসময়ের বর্ষণে কর্দমাক্ত পথঘাট। উর্দিধারীদের পায়ে গামবুট, আবশ্যিক সাবধানতাস্বরূপ।
বডি ওইখানে স্যার, পোঁতা আছে। ভেবেছিলাম, কেউ খুঁজে পাবে না কখনও।
বডি? বডি আর কই? পচেগলে কঙ্কাল, কী-ই বা অবশিষ্ট আর?
একে একে পণ্যবাহী জাহাজ এসে নোঙর ফেলছে খিদিরপুর ডকে। হুগলি নদীর বুকে ভাসমান সার দিয়ে, নিত্যদিনের নিয়মে। পণ্যসামগ্রী যে কত, কত বিচিত্র আকার-আয়তনের যে বাক্স শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে, দেখে তাক লেগে যায় পঞ্চমের। পরিচিত দৃশ্যপট, তবু রোজই ভাবে, এত মালপত্র কোথা থেকে আসে, কারা পাঠায়? ডিউটির পর নদীর ধারে চুপচাপ কিছুটা সময় কাটানো প্রাত্যহিক অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছে তার। বন্ধুরা ঠাট্টা করে, একই জিনিস, জাহাজ আসছে, মাল খালাস হচ্ছে। রোজ কী এত দেখিস?
পঞ্চম নিরুত্তর থাকে। উত্তরটা তার নিজেরও অজানা। কলকাতা বন্দরে সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষীর চাকরিটা যখন পেয়েছিল বেশ কয়েকবছর আগে, সুদূর উত্তর ভারত থেকে পাড়ি দিয়েছিল অজানা-অচেনা বঙ্গদেশে, কখনও ভাবেনি জায়গাটা এত ভাল লেগে যাবে। সব ভাল লাগা ব্যাখ্যা করা যায়?
আজ অবশ্য মনটা ভারী হয়ে আছে। একটু আগে ঝগড়া হয়ে গেল বন্ধুর সঙ্গে।
—আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না পঞ্চম। খুব বেশি হলে আর এক সপ্তাহ সময় দিতে পারি। তার বেশি কিছুতেই নয়।
—তুই তো জানিস, আমি চেষ্টা করছি টাকাটা জোগাড়ের। আর একটু সময় চাই।
—এই কথাটা তো গত দু’মাস ধরে শুনছি। পাঁচ-দশ টাকার ব্যাপার হলে বলতাম না। পাঁচশো টাকা! বাবার থেকে ধার করে দিয়েছিলাম তোকে। শোধ করতে পারবি না জানলে দিতাম না।
—এইভাবে রোজ তাগাদা দিবি জানলে চাইতামও না। চুরি-ডাকাতি না করলে এক ধাক্কায় পাওয়া যায় পাঁচশো টাকা?
—তা হলে চুরি-ডাকাতিই কর! নদীর ধারে বসে জাহাজ গুনলে তো আর টাকা আসবে না!
মাথা গরম হয়ে যায় পঞ্চমের।
—দেব না যা! এক পয়সাও ফেরত দেব না। লেখাপড়া করে তো আর টাকা নিইনি, কোনও প্রমাণ নেই। যা পারিস কর।
—হ্যাঁ, সেটাই করব। টাকা কীভাবে আদায় করতে হয়, আমার জানা আছে। আমার টাকা মেরে দিয়ে কীভাবে চাকরি করিস, দেখব।
—আরে যা যা, মুরোদ থাকলে দেখে নিস যা দেখার!
পঞ্চমের মনে হয়, এতটা মেজাজ গরম না করলেই হত। সত্যিই তো, পাঁচশো টাকা তো কম নয় নেহাত। তবে সে যে চেষ্টা করছে না, এমনও তো নয়। সেটা বুঝবে না? মা-বাবা একসঙ্গে অসুস্থ না হয়ে পড়লে প্রয়োজনও হত না একসঙ্গে অত টাকার। কী করবে এখন? গ্রামের বাড়ির জমিটা বেচে দেবে? বাবা-কাকারা রাজি হবেন?
নদীর ধার থেকে উঠে পড়ে পঞ্চম। হাঁটতে শুরু করে কোয়ার্টারের দিকে। স্ত্রী এবং দুই শিশুপুত্রের জন্য মন কেমন করে ফিরতে ফিরতে। কত দিন দেশের বাড়ি যাওয়া হয়নি। পরের সপ্তাহে সুপারভাইজার সাহেবের কাছে ছুটির দরখাস্ত পেশ করবে স্থির করে ফেলে। কাজে ফাঁকি দেয় না বলে সাহেব পছন্দই করেন তাকে। দেশে গিয়ে জমিজমা বেচার কথাটাও এবার পাড়তে হবে। এভাবে ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে আর কত দিন?
নামেই ঝিল, জলের থেকে কাদারই প্রাধান্য। গভীর রাতে কিঞ্চিৎ শ্রমসাধ্যই ছিল ঝিলের মাঝামাঝি পুঁতে রাখা দেহ উদ্ধার। ‘দেহ’ লিখলাম বটে, বাস্তবে কঙ্কাল। আক্ষরিক অর্থেই। মাংস নেই কণামাত্র। একটি ধুতি এবং ছেঁড়া শার্ট আলগা লেগে রয়েছে। চোয়ালের নীচের অংশ আর বুকের বাঁ দিকের কিছু হাড় নেই। নেই ডান পায়ের মালাইচাকি (Patella), নেই hyoid bone (ঘাড় থেকে চিবুক পর্যন্ত বিস্তৃত অনেকটা ‘U’ আকারের হাড়, যা জিভের নড়াচড়া ও খাবার গলাধঃকরণে সাহায্য করে)। বেশ বোঝা যায়, জায়গাটি কর্দমাক্ত ছিল বলে পচনপ্রক্রিয়াও (decomposition) ঘটেছে দ্রুততর। শেয়াল-শকুনেও পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছে অভাবিত খাদ্যবস্তুর।
মাটি খুঁড়ে পাওয়া পঞ্চম শুক্লার কঙ্কাল
ছেঁড়া শার্টটিতে চারটি বোতাম, পকেটে একটি ছোট লাল পতাকা, সাদা বর্ডারসহ। বন্দরের সশস্ত্র নিরাপত্তাকর্মীদের পোশাকে থাকত যে চিহ্ন। পইতেও রয়েছে অক্ষত। রাত ভোর হলে ঝিলটির সর্বত্র তল্লাশি চালিয়ে কাদার মধ্য থেকে মিলল চোয়ালের হাড়। চুন রাখার একটি ছোট কৌটো, যার উপরে হিন্দিতে খোদাই করা, “ওম জয় হিন্দ”। প্রায় ফুটখানেক লম্বা একটি ছুরিও পোঁতা ছিল কাদাতে, উদ্ধার হল। খুনে ব্যবহৃত অস্ত্র?
পঞ্চম শুক্লা হত্যা মামলা। সাউথ পোর্ট পুলিশ স্টেশনে নথিভুক্ত। তারিখ ২১ মার্চ, ১৯৬০। সে প্রায় ছয় দশক আগের কথা। অভিযোগ খুনের উদ্দেশ্যে অপহরণ এবং হত্যার। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৪ এবং ৩০২ ধারা।
এ মামলায়, শুরুতেই লিপিবদ্ধ থাক, রহস্য উদঘাটনের রুদ্ধশ্বাস রোমাঞ্চ নেই, যা পাঠক সন্ধান করেন গোয়েন্দাকাহিনিতে, সে কাল্পনিক ঘটনাই হোক বা সত্য। নেই একাধিক সন্দেহভাজনের মধ্যে অপরাধীকে চিহ্নিত করার উত্তেজনা।
সমাধানে মেধার ব্যতিক্রমী প্রয়োগ ছিল, এমন দাবি অন্যায্য। অন্যান্য খুনের মামলার তুলনায় কিনারা ছিল সহজসাধ্যই। তবু, কলকাতা পুলিশের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এই মামলা এক চিরকালীন মাইলফলক। শুধু কলকাতাই বা লিখি কেন, সারা দেশেই দিকচিহ্ন তদন্ত-গবেষণায়। কারণ?
কারণ নিহিত, বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার পার্থক্যে | তদন্তপথের দুটি স্পষ্ট বিভাজন থাকে। একটি অভিযুক্তকে চিহ্নিত করা পর্যন্ত, তার গ্রেফতারি পর্যন্ত। যে বিন্দুতে সমাপন কাল্পনিক রহস্যকাহিনির। সত্যজিতের ফেলুদাই হন বা শরদিন্দুর ব্যোমকেশ, নীহাররঞ্জনের কিরীটিই হন বা হেমেন্দ্রকুমারের জয়ন্ত-মানিক, অপরাধটা কে করল এবং কীভাবে করল, তাতেই মূলত সীমাবদ্ধ থাকে রহস্যপিপাসুর কৌতূহল। না লেখকের, না পাঠকের, দায় থাকে না বিচারপর্বের সাতকাহনের। বাস্তবের গোয়েন্দাদের কাছে, লালবাজারের ফেলু-ব্যোমকেশদের কাছে যার গুরুত্ব অপরিসীম।
কিনারা-পরবর্তী কর্মকাণ্ড শাস্তিবিধান নিশ্চিত করতে পারে অভিযুক্তের। আপাতনীরস এবং রোমাঞ্চবর্জিত এক পথ। অতিক্রম করতে ব্যর্থ হলে নিরর্থক যাবতীয় প্রাক্-কিনারা পরিশ্রম। এই পর্বে উত্তেজনার উপাদান যেহেতু সচরাচর থাকে না তেমন, তদন্তের এই অংশটি সম্পর্কে কাল্পনিক গোয়েন্দাগল্পের নিরাসক্তি সহজবোধ্য। আলোচ্য মামলার বিবরণীতে কিনারা-উত্তর অংশটিই প্রধান উপজীব্য।
রোজ কোয়ার্টারে ফিরে আসেন সন্ধে সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে। ১০ মার্চ অন্যথা হল। রাত গড়িয়ে ভোর হল, ভোর গড়িয়ে সকাল, পঞ্চম ফিরলেন না। পঞ্চমের শ্যালকও বন্দরকর্মী ছিলেন। থাকতেন সংলগ্ন কোয়ার্টারেই। খোঁজাখুঁজি এবং উদ্বিগ্ন প্রতীক্ষার পর সাউথ পোর্ট থানায় মিসিং ডায়েরি নথিভুক্ত হল সে-রাতেই।
কারও নিখোঁজ হওয়ার খবর পেলে যা যা করণীয় প্রথামাফিক, করা হল। ওয়ারলেস বার্তা শহরের থানাগুলিতে, কোথাও কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে কি না তার তথ্যতালাশ, নিখোঁজ ব্যক্তির ছবি সংগ্রহ এবং যথাসাধ্য প্রচারের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। ফল হল না, বছর পঁয়ত্রিশের পঞ্চম নিখোঁজই।
পঞ্চম শুক্লা
যত সহকর্মী ছিলেন পঞ্চমের, বন্ধুবৃত্তে ছিলেন যাঁরা, প্রস্তুত হল তালিকা। জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালীনই তাঁদের একজনের থেকে জানা গেল, রামলোচন নামের এক বন্ধুর সঙ্গে কাপড়ের ব্যবসা করার কথা ইদানীং ভাবছিলেন পঞ্চম। বন্দরে সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী, হঠাৎ কাপড়ের ব্যবসা কেন? খোঁজ শুরু হল রামলোচনের। ঠিকানা পাওয়া গেল অচিরেই। তারাতলায় একতলা ফ্ল্যাট তিন কামরার, থাকতেন একাই।
প্রতিবেশীরা জানালেন, ১১ মার্চ ভোরবেলা থেকে রামলোচনকে আর দেখেননি। ঘর তালাবন্ধ। সাদা পোশাকের পুলিশকে লাগানো হল চব্বিশ ঘণ্টার নজরদারিতে।
কিছুদিনের নিষ্ফলা প্রহরার পর ২১ মার্চ ভোররাতে নিজের বাড়িতে চাদরমুড়ি দিয়ে ঢোকার সময় আটকানো হল রামলোচনকে। পুরো নাম রামলোচন আহির। বয়স ত্রিশের কোঠায়, থানায় এনে ঘণ্টাদুয়েকের জেরাতেই প্রকাশ্যে এল পঞ্চম-হত্যার ইতিবৃত্ত।
রামলোচন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। অবাঙালি, কিন্তু বংশপরম্পরায় বাস কলকাতায়। বাবা-ঠাকুরদার পারিবারিক ব্যাবসা ছিল কাপড়ের। রামলোচন ছিলেন ঝুঁকিপ্রবণ প্রকৃতির, শুধুই কাপড়ের ব্যবসায় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখায় আগ্রহী ছিলেন না। নানাবিধ ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে প্রবল উৎসাহ ছিল। বিদেশে পণ্যরফতানির কথাও ভাবতে শুরু করেছিলেন সম্প্রতি। সেই সূত্রে যাতায়াত বেড়েছিল ডক এলাকায়, আলাপ হয়েছিল পঞ্চমের সঙ্গে। যা দ্রুত পরিণত হয়েছিল সখ্যে।
বাবা-মা দেশের বাড়িতে প্রায় একইসঙ্গে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ায় কিছুকাল আগে জরুরি ভিত্তিতে অর্থের প্রয়োজন হয় পঞ্চমের। চিকিৎসা ছিল প্রভূত খরচসাপেক্ষ। শরণাপন্ন হলেন অর্থবান বন্ধুর। বিপদে সাহায্যের হাত বাড়ালেন রামলোচন। পাঁচশো টাকা ধার দিলেন। সে-সময়ে, ছয়ের দশকে, পাঁচশো মানে অনেক টাকা।
গাড়ির যন্ত্রাংশ তৈরির ব্যবসার কথা বেশ কিছুদিন ধরেই ভাবছিলেন রামলোচন, বিনিয়োগও করে ফেলেছিলেন বহুলাংশে। কিন্তু ব্যবসাকে একটা ভদ্রস্থ জায়গায় দাঁড় করাতে আরও অর্থের জোগান একান্ত জরুরি হয়ে পড়েছিল। পঞ্চমের কাছে ধার দেওয়া টাকা ফেরত চাইলেন। পঞ্চম জানালেন, চেষ্টা করবেন শোধ করতে, কিন্তু আপাতত অপারগ।
নিয়মিত তাগাদা শুরু করলেন রামলোচন, তাঁরও আশু প্রয়োজন অর্থের। এই নিয়েই ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে একদিন তীব্র বচসা।
—আমার টাকা চাই তিনদিনের মধ্যে। না হলে পুলিশে যাব।
—যা না, কোনও প্রমাণ আছে? লেখাজোকা তো কিছু হয়নি, আমি পুলিশকে বলব, টাকা নিইনি।
—ঠিক আছে, আমিও দেখাব, আমার টাকা মেরে দিয়ে তুই পার পাবি ভেবেছিস?
—বললাম তো, যা করার করে নিস।
ক্রোধান্ধ রামলোচন সেদিনই স্থির করলেন, পঞ্চম বাঁচার অধিকার হারিয়েছেন। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দেখা করলেন পঞ্চমের সঙ্গে।
—পঞ্চম, তোর সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার পর থেকেই মনটা খারাপ। তুই কিছু মনে করিস না ভাই।
—সে তো আমারও মেজাজটা তেতো হয়ে আছে সেদিনের ঘটনার পর থেকে। আমি কি বলেছি টাকা দেব না?
—আরে ছাড়, যা হওয়ার হয়েছে। আমার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে।
—কী?
—গাড়ির পার্টসের ব্যবসাটা ঠিক জমছে না। কাপড়ের ব্যবসার ঘাঁতঘোঁত আমার হাতের তালুর মতো জানা। ওটাই ভাল করে করব ভাবছি। একজন রাজি হয়েছে টাকা ঢালতে, পরশু বাড়িতে আসবে। তুইও আয়।
—কিন্তু আমি গিয়ে কী করব?
—আরে তুই চাকরির পর ফ্রি-টাইমে লেবার দিবি। হুট করে তো আর টাকার জোগাড় করতে পারবি না। এভাবে শোধ দিবি আস্তে আস্তে। ঝগড়া করে কী লাভ?
পঞ্চম সম্মত হয়ে গেলেন রামলোচনের প্রস্তাবে। নির্ধারিত দিনে রাত আটটায় পৌঁছলেন বন্ধুর বাড়ি। পানাহার হল। দশটা নাগাদ সামান্য অধৈর্য হয়ে পড়লেন পঞ্চম।
—ঘুম পাচ্ছে রে এবার। কখন আসবে তোর ব্যবসায়ী বন্ধু?
—এসে যাওয়ার তো কথা। কেন যে দেরি করছে? মনে হয় আটকে গেছে কোথাও। এক কাজ করি চল, হেঁটে আসি একটু ঝিলের পাশ থেকে, যা গুমোট গরম। পাশেই তো, মিনিট পনেরো হাওয়া খেয়ে চলে আসব। তারপর তুই বাড়ি চলে যাস। আমিও চলে আসব।
—হুঁ … চল।
ঝিলের পাড়ে কিছু সময় কাটল গল্পগুজবে। ঘন হয়ে এসেছে অন্ধকার। রাত সোয়া এগারোটা নাগাদ পঞ্চম বললেন, চল, এবার বাড়ি যাই।
উঠতে যাবেন, সহসা জামার ভিতরে গোঁজা ধারালো ছুরি বার করলেন রামলোচন। চালিয়ে দিলেন পিছন থেকে, পঞ্চমের ঘাড়ে। আকস্মিক আঘাতের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না শক্তসমর্থ চেহারার পঞ্চম, বিস্ময়ের ঘোর কাটার আগেই একের পর কোপ বসিয়ে দিয়েছেন রামলোচন। রক্তাক্ত এবং ভূপতিত পঞ্চমের উপর নির্বিচার ছুরিকাঘাত এর পর, বুকে-পেটে-গলায়। মৃত্যু এল অনিবার্য।
—তারপর?
—ভেবেই রেখেছিলাম আগে। বডিটাকে পুঁতে দিলাম ঝিলের কাদাজলের মধ্যে। জলেই ফেলে দিলাম ছুরিটা, যেটা বাবা শখ করে কিনেছিলেন বেশ কয়েক বছর আগে দিল্লি থেকে। জামার ভিতর গুঁজে নিয়ে গিয়েছিলাম ঝিলে। আমার টাকা দিচ্ছিল না পঞ্চম, আবার রোয়াবও দেখিয়েছিল, মাথার ঠিক ছিল না তাই। ভুল করে ফেলেছি স্যার, স্রেফ রাগের মাথায়।
কলকাতা পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ইনস্পেকটর শ্রীঅনিল ব্যানার্জির উপর পড়ল তদন্তভার। কিনারা সম্পূর্ণ হয়েছে নিঃসংশয়, অপরাধ স্বীকার করেছে অভিযুক্ত। কিন্তু প্রমাণ? ভারতীয় সাক্ষ্য আইন (Indian Evidence Act)-এর ২৭নং ধারায় অভিযুক্তের বয়ান অনুসরণে উদ্ধার হয়েছে কঙ্কাল। মিলেছে ছুরি (weapon of offence)। মৃতের আত্মীয়স্বজন চিহ্নিত করেছেন ধুতি-শার্ট, চুনের কৌটো। কী বাকি থাকে আর?
বাকি যে মূল কাজটাই, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝতে পারছিলেন অনিলবাবু। কঙ্কালটি যে পঞ্চমেরই, তা তর্কাতীত প্রমাণ করা। পরামর্শ করলেন বিশিষ্ট আইনজ্ঞদের সঙ্গে। যাঁরা জানালেন দ্ব্যর্থহীন, অভিযুক্ত যা-ই কবুল করুক পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে, অপরাধের সঙ্গে সংস্রব অস্বীকার করবেই আদালতে, যেমন করে নিরানব্বই শতাংশ ক্ষেত্রে। এবং বেকসুর খালাস পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল, যদি না সন্দেহাতীত প্রমাণ পেশ করা যায় যে কঙ্কালটি পঞ্চমেরই দেহের। এখনও পর্যন্ত প্রমাণস্বরূপ যা রয়েছে হাতে, তা নিশ্চিত চিহ্নিতকরণের পক্ষে অপর্যাপ্ত। সন্দেহের আনুকূল্য অভিযুক্ত পাবেনই, ধরে নিয়ে অগ্রসর হওয়াই সমীচীন।
অনিলবাবু প্রয়াত হয়েছেন বেশ কিছুকাল হল। তাঁর তৎকালীন অধীনস্থ অফিসারদের মধ্যে যাঁরা এখনও জীবিত, তাঁদের সঙ্গে আলাপচারিতায় কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায় আদ্যন্ত কর্তব্যনিষ্ঠ মানুষটির চরিত্রবৈশিষ্ট্যের। স্যার ভিভিয়ান রিচার্ডসের নিস্পৃহ নিধন করায়ত্ত ছিল না হয়তো, কিন্তু মনোভঙ্গি ছিল গাভাসকরের। হাজার প্রতিকূলতার মধ্যেও স্থিতধী সংকল্পে। পরিকাঠামোর সহায়তায় সাফল্যে বিশ্বাসী ছিলেন না, বরং তার সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও শৃঙ্গস্পর্শে ছিলেন একমুখী। নিয়মিত পড়াশোনার অভ্যাস ছিল, দেশবিদেশের অপরাধ-তদন্তের বহমান ধারাটি সম্পর্কে সদাসচেতন থাকতেন পেশাগত উৎকর্ষের তাগিদে।
চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন, কীভাবে হবে কঙ্কালের শনাক্তকরণ? বকেয়া টাকা ফেরত না পাওয়ার আক্রোশে একটা জলজ্যান্ত লোককে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করল, খালাস পেয়ে যাবে? অবসরে অনেকটা সময় কাটাতেন ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে, তৎকালীন ইন্টারনেটহীন সময়কালে জ্ঞানবৃদ্ধিতে গ্রন্থাগারই ছিল মুখ্য ভরসাস্থল। বিদেশে কোথায় একটা এমন মামলা হয়েছিল না? কোথায় যেন পড়েছিলেন? অনিল ছুটলেন আলিপুরে। জাতীয় গ্রন্থাগার যদি দেখাতে পারে কাঙ্ক্ষিত আলোর দিশা।
দিশা মিলল বিস্তর বইপত্র নেড়েচেড়ে। এই তো! এই কেসটাই তো খুঁজছিলেন, “The Buck Ruxton ‘Jigsaw murders’ case”।
মামলার সংক্ষিপ্তসার এই। বাক রাক্সটনের জন্ম ভারতে। নাম ছিল বখতিয়ার রুস্তমজি রতনজি হাকিম। ডাক্তারি পাশ করে চলে যান ইংল্যান্ডে। ওকালতনামা করে নাম পরিবর্তন করেছিলেন। চিকিৎসক হিসেবে রোগীমহলে যথেষ্ট সমাদৃতই ছিলেন। স্ত্রী ইসাবেলা এবং মহিলা গৃহকর্মী মেরি রজারসনকে নিজের ল্যাঙ্কাশায়ারের বাড়িতে কুপিয়ে খুন করেছিলেন। ১৯৩৫-এর সেপ্টেম্বরে।
রাক্সটন নিজে চিকিৎসক ছিলেন, প্রয়োগ করেছিলেন অধীত বিদ্যা। দুটি দেহেরই অগুনতি খণ্ড করেছিলেন। শনাক্ত করার যাবতীয় শরীরচিহ্ন মুছে দিতে চেষ্টা করেছিলেন এক এক করে। খণ্ডগুলি পার্সেলে মুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন স্কটল্যান্ডের একটি ব্রিজের নীচে। উদ্দেশ্য স্পষ্ট, দেহাংশ যদি পরে আবিষ্কৃতও হয়, শনাক্তকরণ যেন হয় অসম্ভব। মোটিভ? যৌন-ঈর্ষা জনিত সন্দেহপ্রবণতা। রাক্সটনের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, ইসাবেলা জড়িয়ে পড়েছেন গভীর পরকীয়ায়। তীব্র অশান্তি হত স্বামী-স্ত্রীর। একাধিকবার সন্তানদের নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলেও গিয়েছিলেন ইসাবেলা। প্রতিবারই ফিরিয়ে এনেছিলেন রাক্সটন। অবিশ্বাস-সন্দেহ-বাদানুবাদ অবশ্য অব্যাহতই থেকে গিয়েছিল। যার চূড়ান্ত পরিণতি ইসাবেলার হত্যায়। এবং ঘটনার সাক্ষী থাকায় গৃহকর্মী মেরিকেও পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ায়।
ঘটনার পক্ষকাল পরে পার্সেলে মোড়া দেহাংশ আবিষ্কার করেন কয়েকজন পথচারী। ছিন্নবিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ছবি তদন্তকারীদের মনে করিয়ে দিয়েছিল ‘Jigsaw Puzzle’-এর কথা। নানা টুকরো জুড়ে একটি পূর্ণ ছবি তৈরি করার খেলা। মামলাটির নামই হয়ে গিয়েছিল ‘Jigsaw Murders’।
একঝাঁক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অসাধ্যসাধন করেছিলেন। দুটি দেহের অসংখ্য খণ্ডাংশ জুড়ে পূর্ণাবয়বে ফিরিয়ে এনেছিলেন, ফরেনসিক প্যাথলজিস্ট অধ্যাপক জন গ্লেইস্টার এবং অ্যানাটমি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জেমস কুপার ব্র্যাশের নেতৃত্বে। ফরেনসিক প্রমাণের এহেন অভিনব এবং সফল প্রয়োগ হয়নি অতীতে। বিশ্বে সেই প্রথম ‘Photographic Superimposition’ ব্যবহৃত হয়েছিল তদন্তে। যা নিশ্চিত চিহ্নিত করেছিল মৃতা দুই মহিলাকে, অকাট্য প্রমাণে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন ডা. রাক্সটন। ফাঁসি হয়েছিল।
কী প্রবল চর্চিত হয়েছিল এ মামলা, কী তীব্র প্রভাব ফেলেছিল জনমানসে, উদাহরণ দিই। ‘Red sails in the sunset’ গানটি তখন তুমুল জনপ্রিয় বিশ্বজুড়ে। বিখ্যাত গীতিকার জিমি কেনেডি লিখেছিলেন। আয়ারল্যান্ডের উত্তর উপকূলে পোর্টস্টুয়ার্ট (Portstewart) শহরে বাড়ি ছিল কেনেডির, সমুদ্র থেকে অদূরে। প্রায়ই দেখতে পেতেন একটি বিলাসবহুল প্রমোদতরী। সেই দৃশ্যই গানটির অনুপ্রেরণা। রাক্সটন মামলা নিয়ে গান পর্যন্ত বেঁধে ফেলা হয়েছিল ‘Red sails…’-এর ছায়ায়।
“Red stains on the carpet/ red stains on the knife Oh Dr Buck Ruxton/ You murdered your wife Then Mary she saw you/ You thought she would tell So Dr Buck Ruxton/ You killed her as well.”
অনিল ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে ছুটলেন ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে (FSL)। মুষ্টিমেয় মামলাতেই তখনও প্রয়োগ হয়েছে ‘Photographic Superimposition’-এর। কিন্তু হয়েছে তো! পঞ্চম শুক্লার ক্ষেত্রে কেন করা যাবে না?
FSL-এর তৎকালীন ডিরেক্টর ছিলেন অধ্যাপক ড. নির্মলকুমার সেন। অনিল সবিস্তার জানালেন, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় কঙ্কাল থেকে লিঙ্গনির্ধারণ হয়ে গিয়েছে। উচ্চতা এবং বয়স-নিরূপণও সম্পূর্ণ। পঁয়ত্রিশ বছরের পুরুষদেহ, পাঁচ ফিট ছয়। যা মিলে যাচ্ছে পঞ্চমের সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে। প্রশ্নাতীত শনাক্তকরণের জন্য, সেই প্রাক-DNA যুগে, রাক্সটন মামলার পদ্ধতির শরণ নেওয়া ছাড়া উপায় কী আর? দেখবেন একবার চেষ্টা করে?
ড. সেন অক্লান্ত পরিশ্রম করলেন। ভারতে সেই প্রথম কোনও মামলার তদন্তে ব্যবহৃত হল ‘সুপারইম্পোজ়িশন’ পদ্ধতি। প্রবাদপ্রতিম চিকিৎসকদের হাতযশে যে কত অভিযুক্ত পর্যবসিত হয়েছে অপরাধীতে, হিসাবের অতীত। আলোচ্য মামলায় যেমন।
সুপারইম্পোজ়িশন কী? সহজ ভাষায়, কোনও এক অবয়বের কোনও একটি জায়গায় একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অন্য একটি অবয়বের ওই জায়গার ওই নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলে যাওয়া, মিশে যাওয়া নিখুঁতভাবে। মানবদেহের ক্ষেত্রে এই বিন্দুগুলিকে বলা হয় nodal point। যা শারীরগত, এবং ব্যক্তিবিশেষে এক এক জনের ক্ষেত্রে ভিন্ন অবস্থান প্রকৃতিগত পার্থক্যে। বিন্দুর সঙ্গে যদি মেলাতে হয় বিন্দুকে, দুটি অবয়বকে একই মাপের, একই আকৃতির করে নেওয়া জরুরি। যে কারণে পঞ্চম শুক্লার পাসপোর্ট সাইজের ছবিটিকে নেগেটিভের সাহায্যে পরিবর্তিত করা হল quarter size-এ। উদ্দেশ্য, খুলির পরিমাপের সঙ্গে ছবির সাযুজ্য স্থাপন।
এখানে দু’-একটি কথা প্রাসঙ্গিক। আমাদের মুখ, নাক, কপাল, চিবুক ও কান আলাদা প্রত্যেকের, হাড়ের গঠন অনুযায়ী। কারও কপাল চওড়া, কারও মাথা বড়। কারও চিবুক ছোট, কারও গলা স্বাভাবিকের তুলনায় মাপে বড়। কাজ করা হচ্ছে দুটি অবয়ব নিয়ে। কপালের একটি নির্দিষ্ট বিন্দু বা nodal point-কে যদি চিবুকের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে বা এক গালের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে যদি অন্য গালের একটি বিন্দুর সঙ্গে এক সরলরেখায় যোগ করা যায় এবং দুটি অবয়বের ক্ষেত্রেই যদি দৈর্ঘ্য এক হয়, তবে বলা যায় যে দুটি অবয়ব একই ব্যক্তির।
পঞ্চম শুক্লার করোটি
পঞ্চমের ক্ষেত্রে কোয়ার্টার সাইজের ছবিটিকে স্থাপন করা হল ক্যামেরার ঘষা কাচের (Ground Glass) নীচে। চিহ্নিত করা হল nodal point সমূহ। রেখাঙ্কিত করে নেওয়া হল অবয়বকে। ছবিটির উপর অতঃপর বসানো হল একটি স্ট্যান্ড। খুলিটিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আনা হল একই অক্ষে। এবং দেখা গেল, খুলির নোডাল পয়েন্টগুলির সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে অবয়বের নোডাল পয়েন্ট। মুখাবয়বের গড়ন, নাক-কান-গলা-চিবুক, সব। প্রাপ্ত খুলি এবং ছবিটি যে একই ব্যক্তির, প্রমাণিত হল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায়। তর্কের অবকাশ ছিল না বিন্দুমাত্র।
মৃত্যুর এগারো দিন পরে উদ্ধার হওয়া কঙ্কাল থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে দেহের শনাক্তকরণ। তা-ও প্রথম বিশ্বের তুলনায় অনগ্রসর দেশে, প্রযুক্তির নিরিখে তুলনায় অনুন্নত পরিসরে, সাড়া পড়ে গিয়েছিল ভারতের পুলিশ মহলে।
বর্তমান সময়ে তদন্তে ‘সুপারইম্পোজ়িশন পদ্ধতির’ কম্পিউটার-নির্দেশিত প্রয়োগ নিতান্ত স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু আজ থেকে প্রায় ছয় দশক আগে, এদেশে অচিন্তনীয় ছিল বিজ্ঞানভাবনার এই অভিনব প্রয়োগশৈলী। যাঁর দূরদৃষ্টি চালিকাশক্তি ছিল সাফল্যের নেপথ্যে, সেই অনিল ব্যানার্জি প্রয়াত হয়েছেন দীর্ঘদিন আগে। কিন্তু জীবদ্দশাতেই স্বীকৃতি পেয়েছিলেন বিজ্ঞানমনস্ক তদন্তের।
ভারতের পুলিশ মহলে তদন্তপ্রক্রিয়ার উৎকর্ষের সিলমোহর পড়ত ‘Indian Police Journal’-এ বিবরণী স্থান পেলে। ডাকসাইটে আইপিএস অফিসার, স্বনামধন্য আইনবিদ বা যশস্বী চিকিৎসক ছাড়া লেখকতালিকায় স্থান পাবেন কেউ, ঘটত কদাচিৎ।
ইনস্পেকটর অনিল ব্যানার্জিকে পঞ্চম শুক্লা হত্যা মামলার নির্যাস পত্রিকায় লিপিবদ্ধ করার সসম্মান আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন সম্পাদকমণ্ডলী। অনিলবাবু লিখেছিলেন তথ্যসমৃদ্ধ নিবন্ধ। শীর্ষক, ‘Camera identifies human skull’। যাতে ধরা ছিল অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলোর আখ্যান, যা আজও অবশ্যপাঠ্য তদন্তশিক্ষার্থীর।
বিচারপর্বে প্রশ্ন উঠেছিল ব্যবহৃত পদ্ধতির আইনি বৈধতা এবং প্রমাণমূল্য নিয়ে, ধোপে টেকেনি। নিম্ন আদালত প্রাণদণ্ড দিয়েছিলেন রামলোচনকে। হাইকোর্ট সাজা হ্রাস করেছিলেন যাবজ্জীবন কারাবাসে। যে রায় অপরিবর্তিত থেকেছিল সুপ্রিম কোর্টে।
কলকাতা পুলিশকে যে তুলনা করা হত স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে, সর্বজনবিদিত। এই অভিধাপ্রাপ্তিতে অবদান আছে তদন্তে বিরল সাফল্যের নজিরসৃষ্টিকারী অসংখ্য মামলার, যার মধ্যে প্রথম সারিতে থাকবে এই পঞ্চম শুক্লা হত্যা। ঘটনাচক্রে যার কিনারা হয়েছিল স্কটল্যান্ডেরই একটি ব্রিজের নীচে পড়ে থাকা দেহাংশের রহস্যভেদ প্রক্রিয়ার অনুসরণে।
অন্য কোথাও নয়, স্কটল্যান্ডে! কী আশ্চর্য সমাপতন!
১.০৪ বণিকবাড়ির অন্তরমহলে
[দেবযানী বণিক হত্যামামলা
তদন্তকারী অফিসার সুজিত সান্যাল]
—থানা থেকে আসছি। দরজাটা খুলুন প্লিজ়!
রাত সোয়া দশটা তখন। কোলাপসিবল গেট পাঁচতলার ফ্ল্যাটের বাইরে। তালা দেওয়া। গেটের পিছনে কাঠের দরজা। যা খোলাই ছিল প্রায় অর্ধেক, পুলিশের ডাকাডাকিতে বন্ধ হয়ে গেল দড়াম।
লোক আছে ভিতরে, একাধিক, বোঝার জন্য বুদ্ধি খাটানোর দরকার হয় না কোনও। নারীকণ্ঠ-পুরুষকণ্ঠ, ফিসফিসানি দিব্যি শোনা যাচ্ছে বাইরে থেকেও। ফের ডাক দেওয়া হল, ‘গড়িয়াহাট থানার ওসি হীরেন্দ্রলাল মজুমদার বলছি, দরজাটা খুলুন একবার।’
ভিতরে যাঁরা ছিলেন, নিরুত্তর। ফিসফিস কথাও শোনা যাচ্ছে না আর। উলটে ওসি-র আওয়াজে নিভে গেল ভিতরের আলো, যেটা জ্বলছিল এতক্ষণ। ডাকাডাকি, দরজায় ধাক্কাধাক্কি আরও বেশ কিছুক্ষণ। ধৈর্যের সীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পর ওসি চূড়ান্ত হুঁশিয়ারি দিলেন, ‘শেষ বারের মতো বলছি। যে বা যাঁরা ভিতরে আছেন, দরজা খুলুন। না হলে ভেঙে ঢুকতে বাধ্য হব, খুলুন!’
তবু কোনও সাড়াশব্দ নেই। ওসি খবর দিলেন দমকলে। অনুরোধ করলেন গেট এবং দরজা ভাঙার জন্য যা যা দরকার, সব নিয়ে দ্রুত চলে আসতে। ২৬, গড়িয়াহাট রোডের পাঁচতলায়। খুব বেশি হলে মিনিটদশেক। যন্ত্রপাতি নিয়ে পৌঁছলেন দমকলকর্মীরা।
লোহার মজবুত কোলাপসিবল গেট। কাঠের দরজাটিও নেহাত পলকা নয়। ভাঙতে সময় লাগল কিছু। ঢুকলেন ওসি-সহ থানার অফিসাররা, দমকলের আধিকারিকরা এবং সাক্ষী হিসাবে চার স্থানীয় বাসিন্দা। যাঁরা জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলেন গড়িয়াহাট মোড়ের কাছে।
এমনিতেই গড়িয়াহাট চত্বর রাতভর আলোঝলমল। ফুটপাথ এখানে বদল হয় না মধ্যরাতে। দোকানপাটের অধিকাংশ সাড়ে ন’টা–দশটার মধ্যে বন্ধ হয়ে গেলেও অন্তত মধ্যরাত পর্যন্ত খোলা থাকেই টুকটাক পান-সিগারেটের ঠেক। দক্ষিণে গোলপার্ক-ঢাকুরিয়া, উত্তরে বালিগঞ্জ ফাঁড়ি-পার্ক সার্কাস। পুবে বিজন সেতু-বালিগঞ্জ স্টেশন, পশ্চিমে রাসবিহারী-চেতলা। মানুষজনের যাতায়াত চলতেই থাকে বেশি রাত পর্যন্ত। গাড়িঘোড়ার স্রোতও তলানিতে ঠেকতে ঠেকতে গড়িয়ে যায় মাঝরাত্তির।
এহেন গড়িয়াহাট মোড় থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বের বহুতলের সামনে পুলিশের গাড়ি, দমকলের সাইরেন সাড়ে দশটা নাগাদ। মাত্রাছাড়া নয়, কিন্তু কৌতূহলী ভিড়-জটলা একটা তৈরি হলই। বাড়তি ফোর্স পাঠানো হল লালবাজার কন্ট্রোল রুম থেকে।
ফ্ল্যাটের ভিতরে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। বিশাল হলঘরে টর্চ ফেলতেই দেখা গেল তিন মহিলাকে, দাঁড়িয়ে আছেন জড়সড়। চোখেমুখে টেনশন আর আতঙ্কের জ্যামিতি। ওসি-র পুলিশি ধমকে আরও কুঁকড়ে গেলেন ওঁরা, ‘কী ব্যাপারটা কী? দরজা খুলছিলেন না কেন? রাতদুপুরে কি আমরা গল্পগুজব করতে এসেছি এখানে?’
গড়িয়াহাট থানা, কেস নম্বর ৪৯, তারিখ ৩০/০১/৮৩। ধারা ১২০বি/৩০২/২০১/৩৪ আইপিসি। অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, খুন, প্রমাণ লোপাট এবং একই অপরাধের উদ্দেশ্যে একাধিকের যৌথ পরিকল্পনা।
সেই তুমুল চাঞ্চল্যকর মামলার বিবরণ। সবে কুড়ির কোঠায় পা দেওয়া এক গৃহবধূর নৃশংস খুন শ্বশুরবাড়িতে। দেবযানী বণিক হত্যা মামলা।
আমাদের কন্ট্রোল রুমে ফোনটা এসেছিল দশটা নাগাদ। আজও অজানা, কে করেছিলেন। বর্তমান সময় হলে বোঝা যেত সহজেই। কন্ট্রোল রুমের সব ফোনেই এখন সিএলআই লাগানো রয়েছে। তখনকার সময়ে ছিল না। ফোনে পুরুষকণ্ঠ জানিয়েছিল, গড়িয়াহাটের বণিকবাড়িতে লোক পাঠান তাড়াতাড়ি। ওদের বড়বউকে সবাই মিলে খুন করেছে। দেরি করলে বডি সরিয়ে দেবে।
থানা থেকে হেঁটে গেলে খুব বেশি হলে তিন মিনিটের পথ, গাড়িতে তার অর্ধেক। কন্ট্রোল রুম জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই ছুটেছিল পুলিশ।
নামেই ফ্ল্যাট, আয়তনের বিচারে প্রায় ফুটবল মাঠ। ঢুকেই প্রশস্ত করিডর, দৈর্ঘ্যে প্রায় একশো মিটার। প্রস্থেও নেহাত কম নয়। করিডরের দু’ধারে সার দিয়ে অনেকগুলি ঘর। যার অধিকাংশেই লাগোয়া বারান্দা। এক কোণে একটি মন্দিরও রয়েছে কাচ দিয়ে ঘেরা। পাঁচতলা থেকে ছ’তলায় সরাসরি যাওয়ার দরজা রয়েছে। আর ছ’তলা থেকে সাততলায় পৌঁছনোরও। চালু হল ঘরগুলির তল্লাশি। ছ’তলা-সাততলা তালাবন্ধ। পাঁচতলার ফ্ল্যাটের একটি ঘরে তিনটি বাচ্চা ঘুমোচ্ছে অঘোরে। অন্য একটিতে এক বৃদ্ধা মহিলা, তিনিও ঘুমন্ত। একটিতে পঞ্চাশোর্ধ্ব এক মহিলা, দৃশ্যতই অসুস্থ। শুয়ে আছেন চোখ বুজে। আর একটি ঘরে বারো বছরের এক ঘুমন্ত কিশোর। রান্নাঘরে তালাচাবি।
করিডরে থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে থাকা তিন মহিলাকে জিজ্ঞাসা করা হল, ‘বাইরে থেকে তো আওয়াজ পাচ্ছিলাম পুরুষকণ্ঠের, ওঁরা কোথায় গেলেন?’ তিনজনই নিরুত্তর, ঠোঁটে যেন কেউ সাইলেন্সার লাগিয়ে রেখেছে। পরের প্রশ্ন, এ বাড়ির বড়বউয়ের নাম কি দেবযানী বণিক? কোথায় উনি? ডাকুন। মুখে এখনও কুলুপ মহিলাত্রয়ীর। ততক্ষণে দুর্গন্ধ পেতে শুরু করেছেন অফিসাররা। পেশার প্রয়োজনে যে গন্ধ ডাক্তার বা পুলিশের অতি পরিচিত। পচতে থাকা মৃতদেহের।
উত্তর-পূর্ব কোণের ঘরটিতে ঢুকতেই গন্ধ তীব্রতর ঠেকল, নাকে রুমাল উঠে এল সবার। শূন্য ঘর, পরিপাটি বিছানা। লাগোয়া বারান্দা। যেখানে ঢোকার মুখেই বাচ্চাদের একটি বড় লোহার দোলনা আড়াআড়ি ভাবে ফেলা রয়েছে। বেশ ভারী, সরানো হল ধরাধরি করে। বারান্দায় একটি ফোল্ডিং খাট। তার উপর স্তূপাকার
লেপ-কম্বল-তোশক ডাঁই করা। সরানো হল।
খাটের নীচেও প্রচুর জামাকাপড়ের জঙ্গল। একদম ঠাসাঠাসি। যা টেনে বার করা হল একে একে এবং ভিতর থেকে বেরোল এক তরুণীর মৃতদেহ। শাড়ি-ব্লাউজ শরীরে। ফুলে উঠেছে দেহ, শুরু হয়েছে পচন। ‘Rigor Mortis’ (মৃত্যুর কিছু ঘণ্টা পর শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শক্ত হয়ে যাওয়া) বাসা বেঁধেছে দেহে। নাকমুখ থেকে রক্তের স্রোত বয়ে শুকনো দাগের চেহারা নিয়েছে শাড়িতে। গলায় ফাঁসের দাগ।
হলঘরে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকা তিন মহিলাকে ডাকা হল। চেনেন এঁকে? সমস্বরে উত্তর, না! ঘুম থেকে তোলা হল বছর বারোর কিশোরকে, চেনো এঁকে? ছেলেটি কেঁদে ফেলল নিমেষে, অস্ফুটে বেরোল একটাই শব্দ— বউদি!
—কী নাম বউদির?
—দেবযানী। দেবযানী বণিক।
খবর পেয়ে গভীর রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছলেন পুলিশকর্তারা। ডিসি হেডকোয়ার্টার, ডিসি ডিডি, ডিসি সাউথ, হোমিসাইড শাখার প্রায় সবাই। তদন্তের চাকা ঘুরতে শুরু করল। তদন্তভার নিলেন হোমিসাইড তৎকালীন শাখার সাব-ইনস্পেকটর সুজিত সান্যাল।
গৃহবধূ-হত্যার খবর জানাজানি হতেই প্রবল প্রতিক্রিয়া শুধু কলকাতায় নয়, রাজ্যজুড়ে। এমন চর্চিত মামলা কমই হয়েছে কলকাতা পুলিশের শতাব্দীপ্রাচীন ইতিহাসে। তখন ইলেকট্রনিক মিডিয়ার আবির্ভাব ঘটেনি। কিন্তু দিনের পর দিন, মাসের পর মাস আনন্দবাজার-যুগান্তরের প্রথম পাতায় আলোচিত হয়েছে দেবযানী-নিধনের রোজনামচা। যা অব্যাহত থেকেছে তীব্র টানাপোড়েনের বিচারপর্বেও। ঘৃণ্য অপরাধের দিকচিহ্ন হিসেবে আজও রয়ে গিয়েছে ওই অভিশপ্ত বহুতল, যাকে স্থানীয় মানুষ চিনতেন ‘বণিকবাড়ি’ নামে। গোলপার্ক থেকে গড়িয়াহাটের দিকে হাঁটতে হাঁটতে, এলাকার ভূগোল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নন, এমন কাউকে এখনও পরিচিতজন দেখিয়ে দেন ওই এগারোতলার মাল্টিস্টোরিড, ‘এটাই সেই বণিকবাড়ি!’
খবরের কাগজের সংবাদ
ওই তিন মহিলার পরিচয় কী, গ্রেফতার হওয়ার পর কী বললেন, বাড়ির পুরুষরাই বা কীভাবে পালালেন, আর ধরা পড়লেন কোথায় কখন, সে বিবরণে পরে আসছি।
তা ছাড়া, এটি তো ‘whodunnit’ নয় যে খুনি কে, জানার কৌতূহল থাকবে। সকলেরই মনে থাকবে, স্বামী-শ্বশুর-দেবর-ননদরা যুক্ত ছিলেন খুনে। চন্দ্রনাথ-চন্দন, এই দুটি নাম অনেকের মনেও আছে নিশ্চিত। তবে ঠিক কোন পরিস্থিতিতে প্রাণ দিতে হয়েছিল ঘরসংসারে আদ্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ এক নেহাতই সহজসরল গৃহবধূকে, কতটা নির্মমতার সাক্ষী ছিল মৃত্যুর আগের ও পরের ঘটনাপ্রবাহ, সে কাহিনিও কম নাটকীয় নয়। বস্তুত, নারীনির্যাতনের এক কলঙ্কময় দলিল। সবিস্তার লিখতে গেলে অণু-উপন্যাসের আকার নেবে, যথাসাধ্য সংক্ষেপে পেশ করলাম দেবযানী-হত্যার ইতিবৃত্ত।
বণিকবাড়ি
শুধু বিত্তবান বললে কম বলা হয়, প্রভূত সম্পদশালী ছিল গড়িয়াহাটের বণিক-পরিবার। ব্যবসা মূলত চা-বাগানের। এ ছাড়াও বহুমুখী ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে ক্রমশ ফুলেফেঁপে ওঠা। গড়িয়াহাটের এগারোতলা ‘বণিকবাড়ি’ তৈরি করেছিলেন চন্দ্রনাথ বণিক।
একতলা থেকে চারতলার ফ্ল্যাটগুলি ভাড়া দিয়েছিলেন বা বিক্রি করেছিলেন। কোনওটা আবাসিকদের, কোনওটা সরকারি–বেসরকারি সংস্থাকে। নিজে থাকতেন সপরিবারে পাঁচতলায়, প্রায় দশ হাজার স্কোয়ার ফিটের ফ্ল্যাটে। ছ’তলা এবং সাততলার ফ্ল্যাট নিজের অধিকারে রেখেছিলেন। আট থেকে এগারো, উপরের চারটি তলা ছিল নির্মীয়মান অবস্থায়।
বণিক পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। চন্দ্রনাথ মধ্যপঞ্চাশ পেরিয়ে ষাট-ছুঁইছুঁই। স্ত্রী কিছুকাল হল অসুস্থ। মা বেঁচে আছেন। তিনিও শয্যাশায়ীই বলা চলে, ওষুধবিষুধ-পরিবৃত জীবন। নয় সন্তানের জনক চন্দ্রনাথ। পাঁচ কন্যা, চার পুত্র। বড়মেয়ে কল্যাণী বিবাহিতা, কসবায় শ্বশুরবাড়ি। তার পরের দু’জন, জয়ন্তী আর চিত্রার বিয়ে হয়েছে যথাক্রমে শিলিগুড়ি আর শ্রীরামপুরে। সুমিত্রা এবং বিত্রা অবিবাহিতা এখনও, থাকেন বাবা-মায়ের সঙ্গে। বড়ছেলে চন্দন বণিক, ১৯৭৫–এর অগস্টে সম্বন্ধ করে বিয়ে হয়েছে বর্ধমানের নতুনগঞ্জ নিবাসী ব্যবসায়ী ধনপতি দত্তের একমাত্র মেয়ে দেবযানীর সঙ্গে। তিন সন্তান চন্দন-দেবযানীর। দুই ছেলে বাবু আর টাবু, মেয়ে মামণি। খুবই ছোট এখনও, শৈশবের চৌকাঠ পেরতে ঢের দেরি। মেজোছেলে আশীষ বিবাহিত, স্ত্রীর নাম রূপা। একটি মেয়ে আছে ওঁদের, সে-ও দুধের শিশুই প্রায়। সেজো অসীম অবিবাহিত। সবচেয়ে ছোট বারো বছরের নন্দন, ক্লাস সেভেন।
বাড়িতে কাজের লোক বলতে জনাপাঁচেক। মাঝবয়সি চৈতন্য, দীর্ঘদিন রান্নাবান্না করেন বণিকবাড়িতে। চারতলার ল্যান্ডিং-এর পাশে একটি ছোট ঘরে থাকেন। যদু নামের যুবক, থাকেন তিনতলায় সিঁড়ির পাশের ঘরে। কাজ বলতে চন্দ্রনাথের সঙ্গে সকালে বাজার যাওয়া, বাসনপত্র ধোওয়া, টুকটাক হাজারো ফাইফরমাশ খাটা। ঊর্মিলা, সকাল-বিকেল ঠিকের কাজ করেন। ঘর মোছা, কাপড় কাচা, রান্নায় সাহায্য ইত্যাদি। পুষ্পা, বয়স কুড়ির এদিক-ওদিক, দেখাশোনা করেন চন্দন-দেবযানীর বাচ্চাদের। আর শান্তি, বারো বছরের কিশোরী। দেখভাল করার দায়িত্ব আশীষ-রূপার একমাত্র মেয়ের।
বর্ধমানের দত্ত পরিবারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিও প্রয়োজন এখানে। খুবই বর্ধিষ্ণু এঁরা। ধনপতি দত্তের রাইস মিল আছে, আছে পেট্রল পাম্পও। অনেকগুলি বসতবাড়ি আছে বর্ধমানে, জমিজমাও যথেষ্ট। আছে মাছের ভেড়িও। স্ত্রী সুধারানী বর্তমান। তিন ছেলে, দেবদাস, বিপ্রদাস এবং রামদাস। এক মেয়ে, দেবযানী। সবার ছোট, বাড়ির সকলে চোখে হারায়। দাদারা ডাকে ‘বোনু’ বলে, মা-বাবার আদরের ডাক ‘বুড়ি’।
আগে লিখেছি, তবু মনে করিয়ে দিই, বণিক আর দত্ত পরিবারের পারস্পরিক আলাপ-দেখাশোনার পর দেবযানীর বিয়ে হয়েছিল চন্দনের সঙ্গে। ৭৫-এর অগস্টে। বাল্যবিবাহই বলা চলে, দেবযানী তখন সবে চোদ্দো। চন্দন সবে কুড়ি পেরিয়েছে। একমাত্র মেয়ের বিয়ে, যৌতুকে কার্পণ্য করেননি ধনপতি। বণিক পরিবারের এ নিয়ে অভিযোগের রাস্তা ছিল না কোনও।
দেবযানী বণিক
বিয়ের প্রথম তিন বছর কোনও সমস্যা ছিল না। সুখী দম্পতির জীবন কাটালেন চন্দন–দেবযানী। ‘বড়বউদি’-র সঙ্গে দেবর-ননদদের সম্পর্কে টাল খায়নি কোথাও। ‘বড়বউমা’-ও স্নেহ থেকে বঞ্চিত হননি শ্বশুর–শাশুড়ির।
তাল কাটতে শুরু করল ’৭৮-এর জুলাইয়ের শেষাশেষি। ধনপতি এসেছেন মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে। চন্দ্রনাথ ও তার স্ত্রী প্রস্তাব দিলেন, ‘আমাদের সেজো মেয়ে চিত্রার বিয়ে দেব এবার। আপনার বড়ছেলে দেবদাসের সঙ্গেই বিয়েটা হোক, আমাদের একান্ত ইচ্ছে।’ ধনপতি সবিনয়ে জানালেন, ‘এই প্রস্তাব আর কিছু দিন আগে দিলে সম্মত হওয়া যেত। কিন্তু এখন তো আর সম্ভব নয়। আপনারা তো জানেন দেবদাসের বিয়ের পাকা কথা হয়ে গিয়েছে গত মাসে আসানসোলের হরিসাধন ঘাঁটির কন্যা কুমকুমের সঙ্গে। অগস্টে বিয়ে। কথার খেলাপ এখন আর করা চলে না।’ বণিক দম্পতি শুনলেন, গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং আর বাক্যব্যয় না করে ভিতরে চলে গেলেন। ধনপতি বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, মেয়ের সঙ্গে কিছু সময় কাটিয়ে ফিরে এলেন বর্ধমানে।
টানাপোড়েনের পরের ধাপও দেবদাসের বিয়ের সূত্রেই। ধনপতি সপরিবারে এসেছেন ছেলের বিয়ের নেমন্তন্ন করতে। ততদিনে দুই পরিবারেরই একে অন্যের আত্মীয়পরিজনের ব্যাপারে সম্যক ধারণা তৈরি হয়ে গিয়েছে। হঠাৎই, কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই চন্দ্রনাথ বললেন ‘আচ্ছা, ড. মৃণালকান্তি বিষ্ণু আপনাদের আত্মীয় না?’ ধনপতি বললেন, ‘হ্যাঁ, আমার ভাইয়ের স্ত্রীর একটিই বোন আছে। ড. বিষ্ণু তাঁর স্বামী। খুবই ঘনিষ্ঠ আমাদের।’ চন্দ্রনাথ শর্ত দিলেন, ড. বিষ্ণুকে বিয়েতে ডাকলে বণিকরা যাবেন না বিয়েতে। ধনপতি জানতে চাইলেন, কেন? জানা গেল, দেবযানীর সঙ্গে বিয়ের আগে, চন্দনের বিয়ের সম্বন্ধ হয়েছিল ড. বিষ্ণুর ভাগনির সঙ্গে। যেদিন মেয়েকে দেখতে আসার কথা, নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় ছ’-সাত ঘণ্টা পর চন্দ্রনাথ গিয়ে জানিয়ে দেন, এ সম্বন্ধ এগোতে আর ইচ্ছুক নন। মেয়েকে না দেখেই। ড. বিষ্ণু বলেন, বিয়ে দেওয়া না-দেওয়া চন্দ্রনাথের ইচ্ছে। কিন্তু এই হেনস্থাটা না করলেই পারতেন। তর্কবিতর্ক-বাদানুবাদ হয়। সেই থেকেই ড. বিষ্ণুর উপর রাগ। ধনপতি শুনলেন সব, কিছু বললেন না।
বিয়ের দিন চন্দ্রনাথ সপরিবারে গিয়ে দেখলেন, ড. বিষ্ণুও আমন্ত্রিত। রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে ধনপতিকে বললেন, ইচ্ছে করে অপমান করলেন বাড়িতে ডেকে। আর কখনও আপনার মেয়ে বাপের বাড়ি আসবে না। ধনপতি বোঝানোর চেষ্টা করলেন, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে না ডাকলে খুবই খারাপ দেখাত। চন্দ্রনাথ কর্ণপাত করলেন না। চলে এলেন বিয়েবাড়ি থেকে।
সংঘাতের তৃতীয় পর্ব বর্ধমানে একটি পুকুর কেনা নিয়ে। ধনপতি পুকুরটি কিনেছিলেন বড় অঙ্কের টাকায়। জানতে পেরে হঠাৎই চন্দ্রনাথ জানান, ওই পুকুরটির জন্য তিনিও বায়না করেছিলেন। তাঁকে দিয়ে দিতে হবে ওই জলাশয়। ধনপতি বললেন, বেশ তো, বায়নানামা দেখান। চন্দ্রনাথ দেখাতে পারলেন না, হালকা বাদানুবাদ হল। দুই পরিবারের মনকষাকষি বাড়ল। যার প্রভাব উত্তরোত্তর পড়তে লাগল দেবযানীর উপর।
দ্রুত পালটে যেতে থাকল শ্বশুর-শাশুড়ি, দেবর-ননদদের ব্যবহার। স্বামী চন্দনেরও। শুরু হল কথায় কথায় কটাক্ষ, দুর্ব্যবহার। মাঝেমাঝেই স্ত্রীর গায়ে হাত তুলতে শুরু করলেন চন্দন। দেবযানী বাপের বাড়ি যেতেন প্রতি দু’মাস অন্তর, সেটা কমে দাঁড়াল ন’মাসে- ছ’মাসে একবার। তা-ও বহু কাকুতি-মিনতির পর। মা-বাবাকে চিঠি লেখা বন্ধ হয়ে গেল বণিকবাড়ির বড়বউয়ের। দেবযানী সহ্য করছিলেন, যেমন করে থাকেন আর পাঁচজন নেহাতই সাদাসিধে, অল্পশিক্ষিতা এবং আর্থিকভাবে স্বামীনির্ভর গৃহবধূ।
পরিস্থিতি জটিলতর হল ’৮২ -র মাঝামাঝি থেকে। বর্ধমানে একটি বিশাল কোল্ড স্টোরেজ কিনলেন চন্দ্রনাথ, ব্যাঙ্ক থেকে কয়েক কোটি টাকা ধার করে। অন্যান্য ব্যবসায় তখন তুলনামূলক মন্দা চলছে বণিকদের। কোল্ড স্টোরেজটি ঠিকমতো চালু হতেও সময় লাগছিল কিছু। জমছিল না তেমন। এদিকে ব্যাঙ্ক থেকে নিয়মিত তাগাদা আসতে শুরু করল ধারের কিস্তি শোধের, বণিকবাড়িতে পৌঁছল ‘ডিমান্ড নোটিস’। চন্দ্রনাথ চাপ দিতে শুরু করলেন ধনপতির উপর, বকেয়া ধারের ২৫ শতাংশ বহন করতে। ওই পঁচিশ শতাংশ মানে সেই তখনকার দিনেও প্রায় পৌনে এক কোটি। ধনপতি জানালেন, তিনি অপারগ। খুব বেশি হলে দশ লাখ। কোিট খানেক মতো দিয়ে ওঠা তাঁর সাধাতীত। উত্তরে চন্দ্রনাথ ফের মুখ খারাপ করলেন যথেচ্ছ। দুই পরিবারের সম্পর্কের কফিনে শেষ পেরেকটি প্রায় পোঁতাই হয়ে গেল।
দেবযানীর জীবন ক্রমে আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠল। বাড়ল চন্দনের মারধরের মাত্রা। শাশুড়ি কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তখন। স্বামী-শ্বশুর-দেবর-ননদরা ‘অলক্ষ্মী’ বলে প্রকাশ্যেই ডাকা শুরু করলেন বাড়ির বড়বউকে। ঘুম থেকে উঠলেই রোজ শুনতে হত, এই অলক্ষ্মীটার মুখ দেখতে হল আবার, সারা দিনটা খারাপ যাবে। এর জন্যই কোল্ড স্টোরেজ চালু হল না। বিস্তর কটাক্ষ, গালিগালাজ। বাড়ির পুরনো রাঁধুনি চৈতন্য খুব স্নেহ করতেন দেবযানীকে। তাঁর হাত দিয়ে গোপনে পাঠানো কয়েকটি চিঠিতে ধরা আছে দেবযানীর নিত্যদিনের যন্ত্রণার কাহিনি।
একটি চিঠির অংশবিশেষ—
শ্রীচরণকমলেষু মা, আমি পাঁচ বছর ধরে সহ্য করছি এদের অত্যাচার। আর পারছি না। আমি এখানে থাকব না আর। তুমি বাবাকে বলো আমাকে নিয়ে যেতে। ওখানে একমাস থাকলে মনটা ভাল হবে। এই চিঠি খুব সাবধানে লিখছি। চৈতন্যদা নিয়ে যাবে। বাবার সঙ্গে ফোনে কথা বললেও এরা পাশে দাঁড়িয়ে শোনে সব। আমার খুব কান্না পায়। তোমার জামাইও ভাল লোক নয়। খারাপ কথা বলে সব সময়, গায়ে হাত তোলে সবার সামনেই। এভাবে থাকা যায় না। বাবাকে আবার বলো, আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে। আমি আর সহ্য করতে পারছি না।
প্রণাম নিয়ো।
তোমাদের বুড়ি।
দেবযানীর সঙ্গে যখন দেখা করতে আসতেন ধনপতি, বসার ঘরে অপেক্ষা করতে হত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মিনিটখানেকের দেখা হত পিতা-পুত্রীর, সাক্ষাতের এবং কথোপকথনের সাক্ষী থাকতেন ননদরা।
লিখতে লিখতে রবীন্দ্রনাথের ‘দেনা পাওনা’ মনে পড়ে অবধারিত— “রামসুন্দর যখন বেহাইবাড়ির অনুমতিক্রমে ক্ষণকালের জন্য কন্যার সাক্ষাৎলাভ করিতেন তখন বাপের বুক যে কেমন করিয়া ফাটে তাহা তাঁহার হাসি দেখিলেই টের পাওয়া যাইতো।”
বাহ্যিক বিচারে দেবযানীর সঙ্গে ‘দেনা পাওনা’-র নিরুপমার মিলের থেকে অমিলই বেশি। নিরুপমার জন্ম অর্থবান পরিবারে নয়। বাবা প্রাণপাত করেছিলেন বকেয়া তিন হাজার জোগাড়ে। নিরুপমার ক্ষয়িষ্ণু মৃত্যু এসেছিল নিজের প্রতি অযত্নে, নিয়ত মানসিক আঘাতে দীর্ণ হতে হতে। দেবযানী বিত্তশালী পরিবারের। খুন হয়েছিলেন। ধনবান পিতাও পারেননি কন্যার শ্বশুরবাড়ির চাহিদা পূরণ করতে।
আপাতভিন্ন প্রেক্ষিত। তবু সার্বিক বিচারে মনে হয়, একটি জায়গায় অক্লেশে মিলেমিশে যান ছাপোষা রামসুন্দর এবং সম্পন্ন ধনপতি। পিতৃহৃদয়ের স্নেহের দোলাচলে। একমাত্র কন্যার মানসিক বা শারীরিক যন্ত্রণালাঘবের ব্যর্থ অসহায়তায়। আর্থিক সামর্থ্য যেখানে তুচ্ছাতিতুচ্ছ।
গল্পের নিরুপমার মৃত্যুর পর “এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়”-এর উপায় ছিল রায়বাহাদুরের। বাস্তবের দেবযানীকে হত্যার পর চন্দ্রনাথদের সে-রাস্তা ছিল না। ঘানি টানতে হয়েছিল জেলের। সান্ত্বনা এটুকুই।
ঘটনায় ফিরি। বিরাশির দুর্গাপুজো শুরু হওয়ার দিন কুড়ি আগের কথা। মেজোছেলে বিপ্রদাসের বিয়ের জন্য মেয়ে দেখতে শিয়ালদার এক আত্মীয়ার বাড়িতে এসে উঠেছেন দত্ত-পরিবারের অনেকে। ধনপতি ব্যবসার কাজে রয়েছেন বর্ধমানেই। বিকেলের দিকে রাইস মিলের ল্যান্ড লাইনে ফোন পেলেন দেবযানীর, ‘বাবা, তোমার জামাই আজ প্রচণ্ড মেরেছে আমায়।’ বলেই কান্না অনর্গল।
ধনপতি সঙ্গে সঙ্গে ফোন করলেন শিয়ালদায় আত্মীয়ার বাড়ি। স্ত্রীকে বললেন, এক্ষুনি যাও বুড়ির বাড়ি। ছুটলেন দত্ত পরিবারের সদস্যরা। বণিকবাড়ির বসার ঘরে পঁয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষার পর দেবযানী এলেন। সঙ্গে ননদরা। একান্তে কথা প্রায় বলতেই দেওয়া হল না বাড়ির লোকের সঙ্গে। সুধারানী লক্ষ করলেন মেয়ের ডানহাতের কনুই ফুলে গিয়েছে। কালশিটের দাগ স্পষ্ট। অনুরোধ করলেন চন্দ্রনাথকে, বুড়িকে কয়েক দিনের জন্য বাড়ি নিয়ে যেতে চাই।
প্রথমে প্রত্যাখ্যাত হল আর্জি, শেষে বহু অনুনয়-বিনয়ের পর চন্দ্রনাথ বললেন, ‘কয়েকদিন পর ব্যবসার কাজে ত্রিপুরা যাবে চন্দন। তখন নিয়ে যাবেন।’
দেবযানীকে কয়েকদিন পর বর্ধমানে নিয়ে গেলেন ভাই রামদাস। মা-বাবাকে মেয়ে জানাল অত্যাচারিত হওয়ার বিস্তারিত কাহিনি। তখনকার দিনে তো বটেই, আজকের দিনেও এদেশের অধিকাংশ মা-বাবারা যা করে থাকেন এই পরিস্থিতিতে, তা-ই করলেন ধনপতি-সুধারানী। বোঝালেন, আমরা কথা বলব চন্দনের সঙ্গে। সব ঠিক হয়ে যাবে, তুই একটু মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা কর বুড়ি।
দেবযানী মা-বাবাকে জানালেন, চন্দ্রনাথ-চন্দন বলেই দিয়েছেন আসার আগে, ধনপতি ওই বকেয়া ধারের ২৫ শতাংশ না দিলে আর কোনও দিন বর্ধমানে আসতেই দেবেন না। ধনপতি বোঝালেন, একসঙ্গে অত টাকা দেওয়া অসম্ভব। দশ লাখ দেবেন বলেছেন তো। পরে আরও চেষ্টা করবেন।
চন্দন এলেন বর্ধমানে দেবযানীকে নিয়ে যেতে। ধনপতি–সুধারানী আপ্রাণ বোঝালেন চন্দনকে, মেয়েকে অত্যাচার না করতে এভাবে। চন্দন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন অভিযোগ শুনে। গালিগালাজ করলেন দেবযানীকে, বললেন আর কখনও বর্ধমানে আসতে দেবেন না। ধনপতি-সুধারানী ভাবলেন, রাগের কথা। সত্যিই যে এটাই এ-বাড়িতে তাঁদের আদরের ‘বুড়ি’র শেষ আসা হতে যাচ্ছে, ভাবেননি দুঃস্বপ্নেও। বেরনোর আগে যখন প্রণাম করছেন দেবযানী, মাথায় আশীর্বাদের হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন ধনপতি, তখনও দূরতম কল্পনাতেও ভাবেননি, মেয়ের সঙ্গে পরবর্তী সাক্ষাৎ হবে মাসকয়েক পরে, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে।
মহালয়ার দিনকয়েক আগে দত্তবাড়ি থেকে পুজোর জামাকাপড় নিয়ে বণিকবাড়ি এলেন দেবদাস। যা তাচ্ছিল্যে ফিরিয়ে দিলেন চন্দ্রনাথ। ফিরে এলেন অপমানিত দেবদাস। ধনপতি বুঝলেন, পুজোটা ভাল কাটবে না বুড়ির।
কাটলও না। অত্যাচার আরও বাড়ল, দেবযানী সম্পূর্ণ একঘরে হয়ে পড়লেন শ্বশুরবাড়িতে। মাঝ-ডিসেম্বরে কোল্ড স্টোরেজের ব্যবসার কিছু কাগজপত্র বর্ধমানের কোর্টে জমা দিতে গিয়েছিলেন চন্দ্রনাথ-চন্দন। আদালতেই দেখা ধনপতিবাবুর বিশ্বস্ত কর্মচারী হৃষিকেশ ঘোষের সঙ্গে। হৃষিকেশকে ডাকলেন চন্দন। নিয়ে গেলেন গাড়ির কাছে, যার মধ্যে বসে আছেন চন্দ্রনাথ। বাকিটা পড়ুন হৃষিকেশের বয়ানে: ‘চন্দ্রনাথবাবু বললেন, তোমার বাবুকে বলবে, আমি প্রতিশোধ নেব। এমন শোধ নেব যে সারা জীবন জ্বলবে। আমি বললাম, আমাকে বলছেন কেন? যা বলার, বাবুকে সরাসরি বলবেন।’
প্রতিশোধ নেওয়াও হল জানুয়ারির শেষাশেষি। ২৮ জানুয়ারি, ১৯৮৩। বণিকবাড়িতে সেদিন আয়োজন হয়েছে সত্যনারায়ণ পুজোর। বাড়িতে প্রচুর আত্মীয়স্বজন। মেজোছেলে আশীষ দিন কয়েক হল সস্ত্রীক শ্বশুরবাড়ি গিয়েছে। এ ছাড়া সবাই উপস্থিত। দেবযানীর দেবর-ননদ, তাঁদের ছেলেপুলে, সব। কাজের লোকের মধ্যে সকালে উপস্থিত যদু, ঊর্মিলা আর শান্তি। চৈতন্য বাড়ি গিয়েছে দিনতিনেক আগে, পুষ্পাও কয়েক দিনের ছুটিতে সুন্দরবনের বাড়িতে।
সকাল ৮-০৫। চন্দনের সঙ্গে হলঘরে কথা-কাটাকাটি হল দেবযানীর। সবার সামনেই চন্দন হিড়হিড় করে টানতে টানতে দেবযানীকে নিয়ে গেলেন বেডরুমে। বেধড়ক মারলেন। কান্না আর আর্তনাদ ছিটকে এল বাইরে। শুনলেন বাড়ির বাকিরা। কোনও উচ্চবাচ্য করলেন না কেউ, কানে তালা দিয়ে পুজোর সিন্নি নিয়ে আলোচনায় ভারী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।
সকাল ৮-৩০। অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে একরকম জোর করেই হলঘরে বেরিয়ে এলেন দেবযানী। ফোন করলেন বর্ধমানের বাড়িতে। তুললেন দেবদাস, বড়ভাই। সেদিন দত্তবাড়ির পুরুষরা সকাল থেকে খুবই ব্যস্ত একটি জমিজমাসংক্রান্ত বিবাদ নিয়ে; একটু পরেই কোর্ট-কাছারিতে ছোটাছুটি আছে। দূরভাষে দেবযানী বললেন, ‘এরা আমাকে মেরে ফেলবে! দাদা, তোরা আজই এসে আমাকে নিয়ে যা।’
দেবদাসের মুখচোখ দেখে ফোন নিলেন ধনপতি। ততক্ষণে দেবযানীর থেকে ফোন কেড়ে নিয়েছেন চন্দ্রনাথ, গালিগালাজ করছেন অকথ্য। ফোন বাবার থেকে আবার নিলেন দেবদাস, বললেন, ‘বোনুকে কিছু করবেন না। আমরা বিকেলের মধ্যে রওনা দিচ্ছি। নিয়ে আসব ওকে। কাকাবাবু, দোহাই আপনার, মারবেন না আর।’ কোনও উত্তর না দিয়ে সপাটে ফোন রেখে দিলেন চন্দ্রনাথ। ঠিক হল, দ্রুত কাজ সেরে সন্ধের আগেই কলকাতায় যাবেন ধনপতি আর দেবদাস। দেবযানীকে নিয়ে আসবেন বাড়িতে। কে জানত, তখনই না বেরিয়ে পড়ে বিকেলে যাওয়ার সিদ্ধান্তের পরিণতি কী ভীষণ মর্মান্তিক হতে যাচ্ছে!
পুজো শেষ হল। সবাই প্রসাদ খেলেন পাত পেড়ে। দেবযানী অভুক্ত থাকলেন, খেতে দেওয়া হল না। পুজোর জায়গার কাছাকাছি আসতেই দেওয়া হল না ‘অলক্ষ্মী’ অপবাদে। অতিথিরা চলে গেলেন দুপুর দুপুর। কল্যাণী আর চিত্রা, বণিকদের বড় আর সেজো মেয়ে, ফিরে গেলেন।
দুপুর গড়িয়ে যখন বিকেল, বণিকবাড়িতে উপস্থিত চন্দ্রনাথ, ছেলেদের মধ্যে চন্দন-অসীম-নন্দন। মেয়েদের মধ্যে জয়ন্তী, সুমিত্রা আর বিত্রা। দেবযানী নিজের ঘরে। চন্দ্রনাথের স্ত্রী আর মা নিজেদের ঘরে বিশ্রামে। বাচ্চারা আছে নিজেদের ঘরে, নিজেদের মতো। কাজের লোকদের মধ্যে রয়েছে যদু আর শান্তি। ঊর্মিলা দুপুরের কাজ সেরে নীচে গিয়েছেন। আবার আসার কথা সন্ধেবেলায়।
বিকেল ৪-০৫। দেবযানীর ঘরে ঢুকলেন চন্দ্রনাথ-চন্দন। কিছু পরেই দেবযানীর পরিত্রাহি চিৎকার ভেসে এল ঘর থেকে। যদু এবং শান্তি, দু’জনেরই খুব প্রিয় ছিল বড়বউদি। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে ছুটল দেবযানীর ঘরের দিকে। হলঘরে আটকে দিলেন সুমিত্রা, ‘তোদের কী দরকার এখানে? যা, কাজে যা!’
দেবযানীর আর্তনাদ স্তিমিত হয়ে এল একটু পরে। সাড়ে চারটে নাগাদ রান্নাঘর থেকে উঁকি দিয়ে যদু দেখল, ওই ঘরে ঢুকছেন অসীম-জয়ন্তী-সুমিত্রা-বিত্রা। কৌতূহল সামলাতে না পেরে ফের যদু আর শান্তি চলে এল ঘরের কাছাকাছি। আবার ধমক সুমিত্রার, ‘তোদের বললাম না নিজের কাজ করতে! যা এখান থেকে।’ যদু আর শান্তি ফিরল রান্নাঘরে। তার আগে অবশ্য দেখা হয়ে গিয়েছে, বড়বউদি ঝুলছে ঘরের সিলিং ফ্যানে। গলায় ফাঁস শাড়ির।
তখন পৌনে পাঁচটা। ধনপতি-দেবদাস কলকাতা রওনা হওয়ার তোড়জোড় করছেন। ফোন বাজল নতুনগঞ্জের বাড়িতে। দেবদাস তুললেন। অন্যপ্রান্তে চন্দ্রনাথ, সকালের রুদ্রমূর্তি বদলে গিয়ে অস্বাভাবিক অমায়িক এখন।
—তোমরা কি রওনা হয়ে গিয়েছ?
—না কাকাবাবু, এই বেরব।
—শোনো, তোমরা আজ এসো না। আমি কাল বর্ধমান যাচ্ছি কাজে। তোমাদের দুর্গাপুরের পেট্রল পাম্পে দেখা করে নেব।
—বোনুকে একবার দেবেন, একটু কথা বলতাম।
—বউমা তো বেরিয়ে গেল একটু আগে চন্দনের সঙ্গে, সিনেমা দেখতে। তোমরা চিন্তা কোরো না, ও ভাল আছে।
ফোন রেখে দেওয়ার পরও খচখচানি একটা থেকেই গেল ধনপতি আর দেবদাসের। ব্যবহারে হঠাৎ এমন ভোলবদল? তারপর ভাবলেন, হতে পারে সকালের মারধরের পর অনুতাপ হয়েছে ওঁদের। মিটমাট হয়েছে সাময়িক। তা ছাড়া কাল তো চন্দ্রনাথ আসছেনই, মুখোমুখি কথা বলে নেওয়া যাবে। অনেক হয়েছে, ঘরের মেয়েকে ফিরিয়ে আনবেন ঘরে।
সন্ধে নেমেছে। বণিকবাড়িতে তখন প্রমাণ লোপাটের ব্যস্ততা। কিন্তু মাথা কাজ করছে না কারও। শান্তি তো রোজ রাত্রে এ বাড়িতে থাকেই, যদুও কখনও কখনও থেকে যায়। শুয়ে পড়ে রান্নাঘরে। দু’জনকেই বলা হল রাত্রে বাইরে শুতে। শান্তি গেল ঊর্মিলার ঘরে, যদু তিনতলায় সিঁড়ির পাশে নিজের রোজকার আস্তানায়। জয়ন্তী ভয় দেখালেন যাওয়ার আগে, ‘কাউকে কিছু বললে কাজ ছাড়িয়ে দেব চুরির বদনাম দিয়ে। না খেতে পেয়ে মরবি।’ ঊর্মিলা সন্ধেবেলা কাজে এসে দেখলেন, কোলাপসিবল গেট বন্ধ। বেল বাজালেন। ভিতর থেকে চন্দ্রনাথ বেরিয়ে এসে বললেন, ‘কাল আসবি। আজ আর দরকার নেই।’
কিল-চড়-লাথি-ঘুসি তো ছিলই যেমন খুশি, লাঠি দিয়েও সজোরে দেবযানীর মাথায় মেরেছিলেন চন্দন। সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলেন দেবযানী। অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণে মৃত্যু তৎক্ষণাৎ। খুনকে আত্মহত্যার চেহারা দিতে এর পর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল সিলিং ফ্যানে। বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল দেবযানীর ঘর। বাচ্চাদের বলা হয়েছিল, মায়ের শরীর খারাপ, ঘুমোচ্ছে। তোমরা অন্য ঘরে থাকো। কতই বা বড় ওরা তখন, বাবার কথা মেনে নিয়েছিল নিষ্পাপ বিশ্বাসে।
রাত গভীর হলে চন্দ্রনাথরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলেন, আত্মহত্যার গল্পটা না-ও দাঁড়াতে পারে। আপাতত দেহ লুকিয়ে ফেলা যাক। ঘরের লাগোয়া বারান্দায় ফোল্ডিং খাটের ভেতর দেবযানীর দেহ পুরে দেওয়া হল। কীভাবে, শুরুতে লিখেছি বিস্তারিত।
পরদিন সকাল। ২৯/১/৮৩। একটি সুটকেস নিয়ে দশটা নাগাদ চন্দ্রনাথ-চন্দন বেরলেন। গোলপার্কের ইন্ডিয়ান ওভারসিজ় ব্যাংক থেকে এক লাখ টাকা তুললেন। এবং সোজা পৌঁছলেন পারিবারিক চিকিৎসক অজিতকুমার ব্যানার্জির চেম্বারে। বললেন, ‘এক মহিলা গৃহকর্মী মারা গিয়েছেন। একটা ডেথ সার্টিফিকেট লিখে দিতে হবে।’ ডাক্তারবাবু বললেন, ‘মৃতদেহ না দেখে সেটা কী করে সম্ভব?’ চন্দ্রনাথ সুটকেস খুললেন, যাতে সদ্য ব্যাংক থেকে তোলা এক লাখ। বললেন, ‘কত লাগবে আপনার?’
টাকার গরমের এই এক মুশকিল, সব কিছুই ক্রয়যোগ্য ভাবায় কখনও কখনও। ডাক্তারবাবু শুনে হাসলেন। সুটকেস বন্ধ করে দিয়ে বললেন, যতই দিন, এ জিনিস আমার দ্বারা হবে না। আসুন আপনারা।
বেরনোর আগে শেষ প্রশ্ন করলেন চন্দ্রনাথ, ‘ময়নাতদন্তে কি বোঝা যায়, খুন, না আত্মহত্যা?’ ডাক্তার ব্যানার্জি বললেন, ‘সে তো যায়ই। খুব সহজ। কিন্তু এ প্রশ্ন করছেন হঠাৎ?’ চন্দ্রনাথ-চন্দন আর দাঁড়ালেন না, ফিরলেন বাড়ির পথে। কন্ট্রোল রুমে সে রাতের ফোনটা কি ডাক্তারবাবুই করেছিলেন? কে জানে!
এদিকে নিয়মমতো ২৯ তারিখ সকালে কাজে এলেন ঊর্মিলা আর যদু। শান্তিও এল, পুষ্পাও ফিরে এসেছে বাড়ি থেকে। ভয় দেখিয়ে কি আর মুখ বন্ধ করা যায় সব সময়? যদু আর শান্তি খুলে বলল ঊর্মিলাকে, আগের দিন বিকেলে যা যা ঘটেছিল, যা যা দেখেছিল, সব। ঊর্মিলা সাহস করে জানতে চাইলেন চন্দনের কাছে, বড়বউদিকে দেখছি না। কোথায়? উত্তর এল, বাপের বাড়ি গিয়েছে গত রাতে। ভাইরা এসে নিয়ে গিয়েছে। বাচ্চারা দেখল, মায়ের ঘর এখনও বন্ধ। চন্দন বোঝালেন, মা বর্ধমান গিয়েছে, কয়েকদিন পরই ফিরবে।
রাত বাড়ল। প্রায় দশটা। ঊর্মিলা কাজ সেরে ফিরে গিয়েছেন। যদুও বেরনোর তোড়জোড় করছে। পুষ্পা আর শান্তি রয়েছে। বেল বাজল ফ্ল্যাটের, থানা থেকে আসছি, দরজা খুলুন প্লিজ়। আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। পাঁচতলা থেকে ছ’তলায় ওঠার দরজা দিয়ে উপরে উঠে গেলেন চন্দ্রনাথ-চন্দন-অসীম। সাফাইকর্মীদের ব্যবহারের জন্য ছিল ঘোরানো সিঁড়ি। নেমে গেলেন নীচে, পালালেন নিঃশব্দে রাসবিহারী অ্যাভিনিউয়ের দিকের গেট দিয়ে। যদু-শান্তি-পুষ্পাকে রান্নাঘরে ঢুকিয়ে চাবি দিয়ে দিলেন সুমিত্রারা। শাসালেন, ‘কিচ্ছু বলবি না পুলিশকে। মারলেও মুখ খুলবি না কেউ।’
পুলিশ ঢুকল দরজা ভেঙে। যা হল এর পর, লিখেছি। কথায় বলে, পাপ বাপকেও ছাড়ে না। সেখানে কে চন্দ্রনাথ, কে-ই বা চন্দন-অসীম? আর কে-ই বা সুমিত্রা-জয়ন্তী-বিত্রা?
চন্দ্রনাথরা পালালেন কোথায়? প্রথমে মহাত্মা গাঁধী রোডের ‘Hoteliers Associates’-এ আগরতলার রমেশ দত্ত পরিচয়ে ঘর নিলেন চন্দ্রনাথ। হোটেলের রেজিস্টারে ছেলেদের নাম লিখলেন সুশীল দত্ত আর অশোক দত্ত। একদিন পরে সেখান থেকে বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিটের শিয়ালদা লজ়। এবার গৌর সাহা নামে রেজিস্টারের ফর্ম ভরতি করলেন চন্দ্রনাথ।
দেবযানী বণিক-এর শ্বশুর চন্দ্রনাথ বণিক
হইচই পড়ে গিয়েছে শহরে ততক্ষণে দেবযানী-হত্যা নিয়ে। পুলিশ সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে পলাতকদের ধরতে। চন্দ্রনাথ-চন্দন-অসীমদের ছবি নিয়ে শহর চষে ফেলছে একাধিক সোর্স। চন্দ্রনাথরা বুঝলেন, বেশিদিন এভাবে পালিয়ে থাকা অসম্ভব। হোটেল থেকে ফেব্রুয়ারির ৪ তারিখ দুই ছেলেকে নিয়ে বেরলেন হাজরার উদ্দেশে, পরিচিত উকিলের বাড়ি। পুলিশ খবর পেল সোর্স মারফত, রাসবিহারী মোড়ের কাছে ৪ ফেব্রুয়ারির দুপুরে আটকানো হল একটি ট্যাক্সি। ভিতরে চন্দ্রনাথ-চন্দন-অসীম। সোজা নিয়ে যাওয়া হল বণিকবাড়ি। যে লাঠি দিয়ে মারা হয়েছিল দেবযানীর মাথায়, উদ্ধার হল ছ’তলার অফিসঘর থেকে। ফাঁস দিতে ব্যবহৃত শাড়ি বেরোল সাততলা থেকে।
পুলিশের কাজই তো অপরাধ-দমন, কিনারা করা ঘটে যাওয়া অপরাধের। তারপর চার্জশিট, বিচারপর্বে সাক্ষ্যদান এবং আরও ‘তারিখ পে তারিখ।’ এবং অনন্ত অপেক্ষা আদালতের আদেশের। রায় পক্ষে গেলে অভিযুক্তের আবেদন উচ্চ থেকে উচ্চতর আদালতে, পুলিশি তদন্তের কাটাছেঁড়া নিয়মমাফিক। এটা করেননি কেন, ওঁর জবানবন্দি নেওয়া হয়নি কেন, সিজ়ার লিস্টে অমুকের নাম নেই কেন, তমুক তখন কোথায় ছিলেন, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সামনে পড়তে হয় কেস ডায়েরিকে। সামান্যতম খুঁত পেলেই তিরস্কার বরাদ্দ।
সংগতই, তদন্ত তো নিশ্ছিদ্রই হওয়া উচিত। ভুলত্রুটি তো নিষিদ্ধই, মামলা যখন খুনের মতো গুরুতর অপরাধের, প্রশ্ন যখন ফাঁসি বা যাবজ্জীবন কারাবাসের। মাননীয় আদালত অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের পরই রায় দেন। যা মেনে নিতে হয় নতমস্তকে।
কিছু মামলা আসে কদাচিৎ, যখন স্রেফ রোজকার পেশাগত দায়বদ্ধতার সীমানার বাইরেও তৈরি হয় দোষীকে শাস্তিদানের বাড়তি মানবিক তাগিদ। দেবযানী মামলাও ছিল এমনই ব্যতিক্রমী। মিডিয়ার ঢক্কানিনাদের জন্য শুধু নয়। ঊর্ধ্বতনের চাপে শুধু নয়। এক নির্দোষ গৃহবধূর নির্মম হত্যাকাণ্ডে যাতে সাজা হয় দোষীদের, নিশ্চিত করতে পেশাগত প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে উঠে দলগতভাবে ঝাঁপিয়েছিল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দফতর। তদন্তকারী অফিসার সুজিত সান্যালের সুযোগ্য নেতৃত্বে। কোনও কোনও বিরল মামলায় অভিযুক্তের অপরাধ সম্পর্কে যখন নিশ্চিত হই আমরা সাক্ষ্যপ্রমাণ-তথ্যতালাশের পর, তখন মনে হয় আমাদের, যা হওয়ার হোক। শেষ পর্যন্ত যাব। শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চলে। চলতেই থাকে।
দুরন্ত লড়েছিলেন তদন্তকারী অফিসার সুজিত সান্যাল। সুজিতের বৈশিষ্ট্য ছিল, এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যেতেন ঘটনার সঙ্গে, নাওয়াখাওয়াও ত্যাগ করতেন কখনও কখনও। তদন্ত শুধু পেশা ছিল না, নেশাও। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে তাঁর অধীনে যাঁরা কাজ করেছেন কোনও না কোনও সময়, তাঁরা আজও শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ান সুজিতবাবুর প্রসঙ্গ উঠলে। গোয়েন্দা বিভাগের বিভিন্ন পদে সুনামের সঙ্গে কাজ করার পর অবসর নিয়েছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার হিসেবে।
বিচার শুরু হল। বিত্রার বিচার শুধু জুভেনাইল কোর্টে, যেহেতু তখনও নাবালিকা। বণিক পরিবার জলের মতো টাকা খরচ করলেন উকিলদের পিছনে। দাবি করা হল, চন্দ্রনাথ-চন্দন-অসীম ঘটনার সময় ছিলেনই না বাড়িতে। ধৃত মহিলারাও নির্দোষ, আর কীসের খুন? দেবযানী তো আত্মহত্যা করেছেন। দীর্ঘ সওয়াল-জবাবে ধোপে টেকার কথা ছিল না এই মিথ্যাচারের। টেকেওনি। যদু-শান্তির সাক্ষ্য তো ছিলই। যে লাঠি দিয়ে মারা হয়েছিল দেবযানীর মাথায়, তাতে হাতের ছাপ ছিল চন্দনের। যে হোটেল দুটিতে ঘটনার পর ঠাঁই নিয়েছিলেন চন্দ্রনাথরা, তার রেজিস্টারের লেখার সঙ্গে চন্দ্রনাথের হাতের লেখা মিলে গিয়েছিল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায়। সর্বোপরি দেবযানীর লেখা চিঠিগুলি তর্কাতীতভাবে প্রমাণ করেছিল ধারাবাহিক নির্যাতন।
আদালতে চত্বরে চন্দ্রনাথ বণিক
আর আত্মহত্যার তত্ত্ব? খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছিল মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক বিভাগের প্রধান ড. রবীন বসুর ময়নাতদন্তের রিপোর্টে। দেহে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন ছিল, প্রতিটির খুঁটিনাটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিল সেই রিপোর্ট। পরিষ্কার বলা হয়েছিল, মাথার আঘাত এতটাই গুরুতর ছিল, চিড় ধরে গিয়েছিল দেবযানীর খুলিতে। এলোপাথাড়ি যত্রতত্র আঘাতের তীব্রতাতেই মৃত্যু, “fissured fracture on the vault of her scull and several other injuries, all ante-mortem and homicidal in nature.” আর গলায় ফাঁসের দাগ, পুলিশি পরিভাষায় ‘ligature mark’? রিপোর্টে স্পষ্ট লেখা ছিল, “post-mortem hanging”। অর্থাৎ, মৃত্যুর পর দেহ ঝোলানো হয়েছিল।
’৮৫-র এপ্রিলে রায় দিলেন আলিপুর কোর্ট। জয়ন্তী, সুমিত্রা আর অসীমের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। চন্দ্রনাথ-চন্দনের ফাঁসির আদেশ। জজসাহেব লিখলেন, “But the part played by accused Chandranath irrespective of his age and that of accused Chandan deserve the severest punishment enjoined by the law and no leniency need be shown to them having regard to the facts and circumstances of the case.”
হাইকোর্টে গেলেন বণিকরা। রায় আংশিক বদলাল। চন্দ্রনাথ-চন্দনের ফাঁসির আদেশ বহাল থাকল। সুমিত্রার যাবজ্জীবনেরও। অসীম আর জয়ন্তীর শাস্তি কমে দাঁড়াল দু’বছরের সশ্রম কারাবাসে।
বল যথারীতি গড়াল সুপ্রিম কোর্টে। যেখানে চন্দ্রনাথ-চন্দনের ফাঁসির আদেশ রদ করে রায় দেওয়া হল যাবজ্জীবন কারাবাসের। ১৪ বছর পর মুক্তি পেলেন চন্দ্রনাথ-চন্দন-সুমিত্রা। চন্দ্রনাথ গত হয়েছেন। বাকিরা বর্তমান। জুভেনাইল কোর্টে বিচারপর্বে দোষী সাব্যস্ত বিত্রাও। সুপ্রিম কোর্টের আদেশে মামলা থেকে মুক্তি পান ঘটনার বছরতিনেক পর।
পড়লেন তো। কী-ই বা বলার আর? বাংলা শব্দকোষকে বড় নিঃস্ব দেখায় বিশেষণ খুঁজতে বসলে। করুণ? হৃদয়বিদারক? না কি মর্মান্তিক? বৃথা চেষ্টা, সব অনুভূতিকে কি আর শব্দের পোশাক পরানো যায়?
ঘটনা যতটা বেদনার, স্থাপনাও ততটাই বেদনাদায়ক ছিল, পরিশেষে স্বীকার করি নির্দ্বিধায়।
১.০৫ লাশই নেই, খুন কীসের?
[অনুরাগ আগরওয়াল হত্যামামলা
তদন্তকারী অফিসার দুলাল চক্রবর্তী]
—আবার বলছি মিস্টার আগরওয়াল, পুলিশকে কিছু জানাবেন না। জানালে পস্তাতে হবে। নাতিকে আর দেখতে পাবেন না কখনও।
—জানাব না। ওকে কিছু করবেন না মিস্টার গুপ্ত, প্লিজ়! বলছি তো, টাকা দেব। যা বলবেন, করব।
—বসুশ্রী সিনেমা চেনেন?
—হ্যাঁ হ্যাঁ, হাজরা মোড়…
—রাইট। সন্ধে ৭টা ২০ নাগাদ গাড়ি নিয়ে আসবেন। বসুশ্রীর কাছে দাঁড় করাবেন। টাকা ব্রাউন পেপারে মুড়ে একটা চওড়া লাল রিবন দিয়ে বাঁধবেন। দেখে যাতে চেনা যায়।
—আচ্ছা… আমার এক কলিগ যাবে…দীনদয়াল উপাধ্যায়।
—ওঁকে বলবেন, গাড়ি থেকে নেমে টাকার প্যাকেটটা হাতে নিয়ে মিনিটখানেক দাঁড়াতে। তারপর আবার গাড়িতে গিয়ে বসতে বলবেন। আমার লোক যাবে গাড়ির কাছে। তাঁকে প্যাকেটটা দিয়ে দিতে বলবেন।
—কিন্তু আমার নাতি…মালতু..
—টাকা পাই, নাতি কাল আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। পুরো আশিই আনছেন তো?
—হ্যাঁ, কিন্তু… একবার যদি ওর সঙ্গে কথা বলা যায়…
—ওকে ঘুমের ওষুধ দেওয়া হয়েছে। ঘুমোচ্ছে।
—কিন্তু…
—কোনও কিন্তু নেই। আপনার সন্দেহ হচ্ছে তো, নাতি সত্যিই আমাদের কাছে কি না। টাকা নেওয়ার সময় আমার লোক আপনার নাতির রিস্টওয়াচটা দিয়ে দেবে আপনার লোকের হাতে।
—আচ্ছা আচ্ছা…
—তা হলে ওই কথাই রইল। পুলিশকে জানালে কিন্তু জেনে যাব, মনে থাকে যেন। সাতটা কুড়ি, বসুশ্রী। ঠিক আছে?
গুলমোহন ম্যানসন, ৬০ মিডলটন স্ট্রিট। ফ্ল্যাট নম্বর ৪৩, পাঁচতলায়। এখানেই দীর্ঘদিনের বাস আগরওয়াল পরিবারের। তেষট্টি বছর বয়সি দেবীলাল পরিবারের মাথা, French Motors-এর চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে কর্মরত। আগরওয়ালদের আদি বাড়ি উত্তরপ্রদেশের গোরখপুরে। দুই ছেলে দেবীলালের। শৈলেন্দ্র আর মুরারিলাল। যাঁরা গোরখপুরেই থাকেন, ইলেকট্রিক্যাল যন্ত্রপাতির পারিবারিক ব্যাবসা দেখাশোনা করেন।
শৈলেন্দ্রর দুই মেয়ে, এক ছেলে। মেয়েরা থাকে গোরখপুরেই, বাবা-মায়ের সঙ্গে। ছেলে অনুরাগ সবচেয়ে ছোট, ডাকনাম মালতু | কলকাতায় দাদু-ঠাকুমার কাছে থেকে পড়াশোনা করে। বয়স চোদ্দো, এলগিন রোডের জুলিয়ান ডে স্কুলে ক্লাস সিক্স, সেকশন ই। দেবীলালের ছেলেরা সপরিবারে মাঝে মাঝে আসেন কলকাতায়, সময় কাটিয়ে যান মা-বাবার সঙ্গে।
দাদু-ঠাকুমার নয়নের মণি অনুরাগ, বিশেষ করে দাদুর। চোখে হারান নাতিকে। মালতুও অসম্ভব ন্যাওটা দাদুর। যত রাগ-অভিমান-বায়না-আবদার ওই দাদুর কাছেই। বাবা-মা অনেকবার চেয়েছেন গোরখপুরে নিজেদের কাছে নিয়ে যেতে, ওখানের স্কুলে ভরতি করে দিতে। অনুরাগ রাজি হয়নি | দেবীলাল মুখে কিছু বলেননি, কিন্তু নাতির ইচ্ছায় মনে মনে আহ্লাদিত হয়েছেন খুব।
সালটা ১৯৮৮। সেপ্টেম্বরের শেষদিকে তীর্থযাত্রায় বেরলেন দেবীলাল। স্ত্রী অসুস্থ, একাই গেলেন। গোরখপুর থেকে সস্ত্রীক শৈলেন্দ্র চলে এলেন কলকাতায়, বড়মেয়ে সংগীতাকে সঙ্গে নিয়ে। বাবা যে ক’দিন বাইরে, মায়ের দেখাশোনার প্রয়োজন। তার উপর অনুরাগ রয়েছে।
অনুরাগের তখন পুজোর ছুটি চলছে। দুপুর-বিকেলে কাছেপিঠে প্রায় রোজই বন্ধুদের সঙ্গে এদিক-সেদিক ঘুরতে যেত। কখনও চিড়িয়াখানা, কখনও ভিক্টোরিয়া, কখনও জাদুঘর। ফিরে আসত সন্ধে নামার আগেই।
১২ অক্টোবর দুপুরে দিদি সংগীতা হঠাৎ খেয়াল করলেন, ভাই নিজের ঘরে নেই। কোথায় গেল? মা-কে জানালেন| খোঁজ খোঁজ। বহুতলের দারোয়ানের থেকে জানা গেল, অনুরাগকে দেখেছেন দুপুর একটা নাগাদ কাঁধে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগ নিয়ে বেরতে| মা আর দিদি ভাবলেন, বন্ধুদের সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা করতে গিয়েছে কোথাও। না জানিয়ে বেরনোর জন্য বাড়ি ফিরলে বকাবকি করবেন, ভেবে রাখলেন দু’জনেই।
কিন্তু ফিরলে তো? বিকেল পেরিয়ে সন্ধে, সন্ধে গড়িয়ে রাত। ফিরল না অনুরাগ। স্কুলের বন্ধুদের বাড়িতে ফোন করা হল, শৈলেন্দ্র প্রতিবেশীদের নিয়ে চষে ফেললেন পার্ক স্ট্রিট-ভিক্টোরিয়া-চিড়িয়াখানা চত্বর-প্রিন্সেপ ঘাট-ইডেন গার্ডেন। নেই, কোত্থাও নেই। বিনিদ্র রাত কাটল আগরওয়াল পরিবারের।
পরের দিন সকালে দেবীলাল ফোন করলেন কলকাতার বাড়িতে, বাইরে গেলে রোজ যেমন করে থাকেন। শুনলেন দুঃসংবাদ, ছেলেকে বললেন অবিলম্বে পুলিশে মিসিং ডায়েরি করতে। এবং পত্রপাঠ রওনা দিলেন কলকাতায়। পার্ক স্ট্রিট থানায় ১৩ অক্টোবর জমা পড়ল অনুরাগের ছবি, ডায়েরির পর প্রাথমিক খোঁজখবর শুরু করল পুলিশ। আজ থানায় ছবি পাঠানো, কোথাও কোনও দুর্ঘটনা হয়েছে কি না ইত্যাদি।
১৪ অক্টোবর, সকাল ১০টা। দেবীলাল ততক্ষণে পৌঁছে গিয়েছেন গোরখপুরে। কলকাতার ট্রেন ধরবেন | হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ঢুকতে ঢুকতে রাত সাড়ে এগারোটা হবে। গোরখপুর স্টেশন থেকেই ফোন করলেন বাড়িতে। এবং খবর শুনে মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল। গলা কাঁপছে শৈলেন্দ্রর, জানালেন, এক ঘণ্টা আগে ‘মিস্টার গুপ্ত’ নামে একজন ফোন করে জানিয়েছেন, অনুরাগকে তাঁরা কিডন্যাপ করেছেন। মুক্তির বিনিময়ে দাবি এক লাখ টাকা। পুলিশকে কিছু জানালে মালতুকে প্রাণে মেরে ফেলবে বলে হুমকিও দিয়েছেন |
ফের ফোন এলে একদিন সময় চেয়ে নিতে বললেন দেবীলাল| পরামর্শ দিলেন পুলিশকে এখনই কিছু না জানাতে| আরও বললেন, ব্যাংক থেকে তিরিশ হাজার টাকা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুলে নিতে। বন্ধুবান্ধবদের থেকে বাকিটাও জোগাড় করে রাখতে।
১৪ তারিখই ফোন এল আরও কয়েকবার। হুমকি, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে টাকা না পেলে মেরে ফেলা হবে অনুরাগকে। সঙ্গে রুটিন সতর্কবার্তা, পুলিশকে জানালে পরিণতি মারাত্মক হবে। শৈলেন্দ্র বললেন, বাবা বাইরে আছেন। একটু সময় চাই।
দেবীলাল বাড়িতে ঢুকলেন মাঝরাতে। অফিসের সহকর্মী আর আত্মীয়স্বজনে বাড়ি ভরতি। আশঙ্কা আর আতঙ্কে পুরো পরিবার প্রায় আচ্ছন্ন তখন। French Motors-এর সহকর্মীরা যে যত পেরেছেন, টাকা নিয়ে এসেছেন, শৈলেন্দ্র টাকা তুলেছেন ব্যাংক থেকে। দেখা গেল, আশি হাজার জোগাড় হয়ে গিয়েছে।
পরের দিনের সকাল, ১৫ অক্টোবর। ঠিক ন’টায় ফোন বাজল। অন্যদিকে মিস্টার গুপ্ত |
—কী ঠিক করলেন? বেশি সময় নেই আমাদের হাতে।
—আপাতত আশি হাজার দিচ্ছি। বাকিটা দু’-একদিনের মধ্যে দিয়ে দেব।
—হুঁ, টাকা রেডি রাখুন, কখন কীভাবে কোথায় দেবেন, সন্ধেবেলা জানিয়ে দেব।
—কিন্তু মালতুর সঙ্গে একবার…
—বলছি তো, টাকা পেলে পরশু দিন বিকেলে বাড়ি পৌঁছে যাবে।
কেউ কেউ বললেন, পুলিশে জানিয়ে রাখা যাক। রাতভর আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হল, টাকা দেওয়া হোক। মালতু আগে বাড়ি ফিরুক, তারপর পুলিশে জানানোর কথা ভাবা হবে। ঘরের ছেলের প্রাণ আগে, না অপরাধীর ধরা পড়া আগে? না কি টাকা আগে? আগে মালতু ফিরুক।
অপহরণের মামলায় এই এক মুশকিল। একবার নয়, বারবার দেখেছি আমরা। জানাজানি হয়ে গেলে, মিডিয়ায় প্রচারিত হয়ে গেলে অন্য কথা। কিন্তু যদি সেটা না হয়, জানতে না পারে কেউ পরিবার-পরিজন ছাড়া? মুক্তিপণ চেয়ে ফোন এলে, পুলিশকে জানালে অপহৃতকে প্রাণে মেরে ফেলার ভয় দেখালে, স্বাভাবিক দোলাচলে ভুগতে থাকে পরিবার। পুলিশকে জানাব কি জানাব না?
সত্যি বলতে, দোষও দেওয়া যায় না ভুক্তভোগী পরিবারকে| এ তো চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই-শ্লীলতাহানি নয় যে অভিযোগ করে দিলাম, এবার পুলিশ যা করার করুক। প্রিয়জন জীবিত অবস্থায় অন্যের হেফাজতে বন্দি| এবং যে বা যাদের হাতে বন্দি, জানা নেই তারা কতটা বিপজ্জনক, কতটা মরিয়া। এমন অবস্থায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাথমিক স্তরে পুলিশে অভিযোগ করা থেকে বিরত থাকতেই পছন্দ করে অপহৃতের পরিবার, অভিজ্ঞতা আমাদের। অনেকে মুক্তিপণ দিয়ে প্রিয়জন বাড়ি ফেরার পরই পুলিশকে জানান, কেউ কেউ আদৌ জানানই না।
এক্ষেত্রেও ভয় পেয়েছিলেন আগরওয়াল পরিবার। পুলিশে জানালে পাছে ক্ষতি হয়ে যায় অনুরাগের, সেই আশঙ্কায় মুক্তিপণের টাকা দিয়েছিলেন। যখন জানালেন, তখন চূড়ান্ত ক্ষতি হয়ে গিয়েছে, যা পূরণ হওয়ার নয়।
পুলিশের দিকটাও বলা দরকার। অভিযোগ যদি সাহস করে কেউ করেও ফেলেন অপহরণের, সাবধানে, খুব সাবধানে পা ফেলতে হয় পুলিশকে। মাথায় রাখতে হয়, অপরাধী তো ধরতে হবেই, কিন্তু নিরপরাধ প্রাণের মূল্যে নয়। অপহৃত ফিরে আসুক নিরাপদে, তারপর ঝাঁপানো যাবে, এই ভাবনা কাজ করেই। রক্ষণ মজবুত করে তবেই আক্রমণে যাওয়া। গ্রেফতার, মুক্তিপণের টাকা উদ্ধার, এসব পরেও হতে পারে, বিলক্ষণ সম্ভব। কিন্তু অপহৃতের প্রাণহানির ন্যূনতম ঝুঁকি থাকতে পারে, এমন কিছু করার আগে হাজারবার ভাবি আমরা|
ঠিক হল,বাড়ির বিশ্বস্ত ড্রাইভার ভবন শর্মাকে নিয়ে দেবীলালের দীর্ঘদিনের সহকর্মী দীনদয়াল উপাধ্যায় টাকা নিয়ে যাবেন। ফোন এল সাড়ে ছ’টায়| যা কথোপকথন হল, কাহিনির শুরুতে পড়েছেন। হাজরা মোড়ে রওনা হলেন দীনদয়াল উপাধ্যায়। যেমনটা নির্দেশ এসেছিল, অক্ষরে অক্ষরে মেনে। কতটুকুই বা দূরত্ব মিডলটন স্ট্রিট থেকে হাজরার? দীনদয়াল যখন পৌঁছলেন বসুশ্রীর সামনে, ঘড়িতে সাতটা দশ। মানে এখনও হাতে মিনিট দশেক। নেমে দাঁড়ালেন, হাতে প্যাকেট। ব্রাউন পেপারের, লাল রিবন দিয়ে বাঁধা। ভিতরে আশি হাজার নগদ| গাড়িতে গিয়ে বসলেন কয়েক মিনিট পর। ঘড়ির কাঁটা সোয়া সাতটা ছুঁয়ে ফেলেছে তখন।
দোকানবাজারের হইহল্লা, গাড়িঘোড়ার ভিড়ভাট্টা, অফিসফিরতি জনতা পিলপিল। ভরসন্ধের হাজরা মোড় গমগম করছে তখন, যেমন করে আজ-কাল-পরশু। কাঁটায় কাঁটায় সাতটা কুড়িতে গাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল বছর দশেকের একটি ছেলে। খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন দীনদয়াল। নাহ্, চেহারায় বিশেষত্ব বলতে কিছু নেই। নোংরা শার্ট, ঢিলেঢালা হাফপ্যান্ট, পায়ে চটিও নেই। নেহাতই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে, বুঝতে বুদ্ধি খরচের প্রয়োজন নেই।
হাফপ্যান্টের পকেট থেকে একটা রিস্টওয়াচ বার করল ছেলেটি। দীনদয়াল হাতে নিয়ে দেখালেন ড্রাইভার ভবনকে| দেখেই ঘাড় নাড়ল ভবন, মালতু ভাইয়া কি হি হ্যায়। শুনে আর একটা কথাও খরচ করলেন না দীনদয়াল। হাতবদল হয়ে গেল ব্রাউন পেপারের প্যাকেট। যেটা নিয়েই দৌড় দিল ছেলেটি, মিশে গেল থিকথিকে ভিড়ে।
পৌনে আটটা নাগাদ মিডলটন স্ট্রিটে ফিরলেন দীনদয়াল। রিস্টওয়াচ দেখে আর এক প্রস্থ কান্নাকাটি শুরু হল। Citizen Quartz white dial, এ ঘড়ি মালতুরই। নিউ মার্কেট থেকে নাতিকে কিনে দিয়েছিলেন দাদুই| মা-দিদি-ঠাকুমার অঝোর কান্না থামালেন শৈলেন্দ্র, টাকা দেওয়া হয়েছে। মালতু কালই ফিরে আসবে। জানতেন না, ওই আশ্বাসবাণী কত ঠুনকো শোনাবে মাত্র এক ঘণ্টা পরে!
আগরওয়ালদের বাড়িতে ফোন বাজল রাত ন’টায়। তুললেন দেবীলাল, অন্যপ্রান্তে পরিচিত গলা। মিস্টার গুপ্ত।
—কী হল মিস্টার আগরওয়াল! টাকা তো পেলাম না।
—মানে? পেলেন না মানে? উপাধ্যায় প্যাকেট দিয়েছে একটা বাচ্চা ছেলের হাতে। ছেলেটা মালতুর ঘড়িও দিয়েছে।
—ছেলেটাকে আর খুঁজে পাচ্ছি না | চালাকি করবেন না আমাদের সঙ্গে।
—কী বলছেন আপনি? দিস ইজ় অ্যাবসোলুটলি ফলস। আপনি কথা দিয়েছিলেন, মালতুকে ছেড়ে দেবেন টাকা পেলে।
—টাকা পেলে দেব বলেছিলাম। টাকাই তো পাইনি!
ফোন কেটে দেওয়ার শব্দ পান দেবীলাল, বসে পড়েন মাথায় হাত দিয়ে|
এবার? কী করণীয়? ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিল পরিবার। পুলিশকে জানাতেই হবে, রাস্তা নেই এ ছাড়া| মামলা দায়ের হল পার্ক স্ট্রিট থানায়। তদন্তের দায়িত্ব পড়ল গোয়েন্দা দফতরের তৎকালীন সাব-ইনস্পেকটর দুলাল চক্রবর্তীর উপর। যিনি সফল কর্মজীবনের শেষে অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার হিসেবে অবসর নিয়েছিলেন।
অনুরাগ আগরওয়াল অপহরণ ও হত্যা মামলা। পার্ক স্ট্রিট থানা, কেস নম্বর ৬৩১, তারিখ ১৭ অক্টোবর, ১৯৮৮। ১২০ বি/৩৬৮/৩৮৪/৩০২/২০১ আইপিসি। অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, খুনের উদ্দেশ্যে অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, খুন এবং প্রমাণ লোপাট। এই মামলা, বহুব্যবহারে মরচে পড়ে যাওয়া তুলনাতেই বলি, কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের টুপিতে উজ্জ্বল পালক। যে মামলা প্রসঙ্গে মাননীয় কলকাতা হাইকোর্ট মন্তব্য করেছিলেন, “The prosecution case as aptly observed by the learned Trial Judge reminds us of a story taken from a thriller.”
অনুরাগ আগরওয়াল
ঘটনা আটের দশকের শেষাশেষির। যাঁরা এখন চল্লিশের কোঠায়, তাঁরা নিশ্চয় ফিরে দেখতে পাবেন সময়টা, অনায়াসে। আজকের মতো হাজার খানেক টিভি চ্যানেল ছিল না তখন। ছিল না ২৪ x ৭ শুধু সিরিয়াল-সিনেমার জন্যই নির্দিষ্ট গোটা পঞ্চাশ বাংলা-হিন্দি-ইংরেজি চ্যানেল। খেলা বা খবরের জন্যও বরাদ্দ থাকত হাতে গোনা গুটিকয়েক। সপ্তাহে একদিন হাপিত্যেশ করে বসে থাকা ‘চিত্রহার’-এর অপেক্ষায়। হিন্দি সিনেমার জনপ্রিয় গানের অনুষ্ঠান। শেষ হয়ে গেলে আক্ষেপ, মাত্র চার-পাঁচটা গান দেয়, এত বিজ্ঞাপনের কী দরকার? স্কুল-কলেজ-পাড়ায় আলোচনা অবধারিত পরের দিন, এ বারেরটা জমল না তেমন, বা শেষ গানটায় পয়সা উসুল!
তখন সিরিয়াল বলতে ’৮৪-র ‘হামলোগ’, ভারতীয় টেলিভিশনের ইতিহাসে প্রথম সোপ অপেরা। যা আবির্ভাবেই তুমুল জনপ্রিয়। প্রতি এপিসোডের শেষে অশোককুমারের কয়েক মিনিটের ভাষ্য আর অননুকরণীয় ‘হামলোগ’ দিয়ে শেষ করা। বছর দুয়েক পরে বোকাবাক্সের পরদা দখল করবে ‘বুনিয়াদ’, দেশ ভাগের পটভূমিতে তৈরি সিরিয়াল | অলোকনাথ আর অনিতা কানওয়ারের হাত ধরে ‘মাস্টারজি’ আর ‘লাজোজি’ ঢুকে পড়বেন আম ভারতীয় পরিবারের হেঁসেলে। সোপ অপেরার সৌজন্যে হাট করে খুলে যাবে বহুদিনের বন্ধ থাকা একটা দরজা। যার জেরে পরের কয়েক দশকে ভারতীয় টেলিভিশনে আছড়ে পড়বে সিরিয়াল-সুনামি।
প্রিয় পাঠক-পাঠিকা, উপরের দুটো অনুচ্ছেদ বাড়তি মনে হতে পারে। কিন্তু প্রেক্ষিতের স্বার্থে প্রয়োজন ছিল। অনুরাগের কথায় ফিরি। জন্ম ’৭৪-এ। বেঁচে থাকলে বয়স হত মাঝচল্লিশ। সিরিয়াল-সিনেমার আকর্ষণ কৈশোরে অনেকেরই থাকে। অনুরাগেরও ছিল, কিন্তু অস্বাভাবিক বেশি মাত্রায়। টিভির পোকা বললে প্রায় কিছুই বলা হয় না। সিরিয়াল-সিনেমা দেখা অনুরাগের কাছে ছিল সাধনার মতো। ডায়লগ মুখস্থ করত, ঘরে অভিনয় করত আয়নার সামনে, পড়াশোনা–খেলাধুলোর মতো নেহাতই ‘তুচ্ছ’ জাগতিক বিষয়ে মাথা ঘামাতে তীব্র অনীহা ছিল বছর চোদ্দোর কিশোরের। আশা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ-আহ্লাদ বলতে একটাই, রুপোলি পরদায় মুখ দেখানো। সেটাই কাল হবে, কে ভেবেছিল?
কারা করেছিল অপহরণ? কীভাবে? কাহিনি পিছিয়ে যাক কয়েক মাস আগে, কিডন্যাপ-কাণ্ডের পান্ডাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।
দেবাশিস ব্যানার্জি, বয়স তখন তিরিশ ছাড়িয়েছে| বাড়ি তিলজলার সি এন রায় রোডে। জীবিকা বলতে ছোটখাটো অর্ডার সাপ্লাই। বাবা মারা গিয়েছেন, মা কিছু টাকা পেনশন পান ‘পলিটিক্যাল সাফারার’ হিসেবে। মধ্যবিত্ত পরিবার, সচ্ছল নয় একেবারেই। যাদবপুরে একটি সাংস্কৃতিক সংগঠনের কাজকর্মে যুক্ত ছিলেন দেবাশিস। সেখানেই ’৮৬ -তে আলাপ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী কাবেরীর সঙ্গে। আলাপ গড়াল প্রেমে, ’৮৮–র জানুয়ারিতে দিনক্ষণ ঠিক হয়ে গেল বিয়ের।
বিয়ের খরচাপাতির ব্যবস্থা করতে গিয়ে টাকাপয়সার সমস্যা দেখা দিল। কিন্তু সব পাকাপাকি হয়ে গিয়েছে, দিন আর পিছনো যায় না। বিয়েতে ধারদেনা হল কিছু। যা ক্রমে বাড়তে থাকল বিয়ের পর, লোকলৌকিকতা ইত্যাদিতে। ব্যবসাতেও মন্দা চলছে তখন। সংসার চালাতে দেবাশিসের নাভিশ্বাস উঠল মাসছয়েকের মধ্যেই। মেজোশ্যালক রেলে কনট্র্যাক্টর ছিলেন, চেষ্টা করলেন দেবাশিসকে কিছু অর্ডার পাইয়ে দেওয়ার। সুবিধে হল না তেমন। শ্যালকের থেকে দেবাশিস ধারও নিলেন হাজার বিশেক, শোধ করতে পারলেন না। কাবেরী প্রায়ই দুঃখ করতেন, দাদার টাকাটা ফেরত দিয়ে দাও, বাপের বাড়িতে লজ্জায় মাথা কাটা যায় আমার।
কসবার মসজিদবাড়ি লেনে থাকতেন দেবাশিসের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বিজন বড়ুয়া, বিজ্ঞানের স্নাতক। প্রাইভেট টিউশন এবং একটি ওষুধের দোকানে টুকটাক কাজ করেই যাঁর দিনগুজরান। অবিবাহিত, একাই থাকেন। আর্থিক অবস্থা করুণ বিজনেরও। ধারদেনা তাঁরও বিস্তর।
দুই বন্ধু সান্ধ্য আড্ডায় প্রায়ই ভাবতেন, এভাবে তো আর চলে না, দেনার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে কতদিন আর টানা যাবে এভাবে? টাকার দরকার, কিন্তু কে দেবে? রাতারাতি লটারি লেগে যাবে, এমন সম্ভাবনা নেই। চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই পোষাবে না। তা হলে? কথায় কথায় একদিন মাথায় এল, কিডন্যাপিং করলে কেমন হয়? চটজলদি বড়লোক হওয়ার আর তো কোনও উপায় দেখা যাচ্ছে না।
ছক কষা শুরু করলেন দুই বন্ধু। কয়েকটা ব্যাপার ঠিক করে নিলেন প্রথমেই। এক, বিশাল ধনী কোনও পরিবারের ছেলেকে টার্গেট করা ঝুঁকির হয়ে যাবে। কাগজে বেরবে, জানাজানি হবে, পুলিশ ঝাঁপাবে। তার চেয়ে ভাল, মোটামুটি সম্পন্ন পরিবারের কাউকে কিডন্যাপ করা। টাটা–বিড়লা জাতীয় নয়, কিন্তু মুক্তিপণ দেওয়ার মতো টাকা আছে, এমন। দুই, যা করতে হবে, ভুলিয়েভালিয়ে। জোরজার করে নয়। তিন, অপহৃতকে রাখার জায়গা চাই। দেবাশিস বললেন বিজনের বাড়িতে রাখার কথা। বিজন শুরুতে গররাজি হলেও মেনে নিলেন শেষ পর্যন্ত| চার, কিছু সরঞ্জাম চাই। মুখ বাঁধার জন্য লিউকোপ্লাস্ট কিনলেন দেবাশিস, বাগরি মার্কেট থেকে air purifier mask। ভাবনা, কিডন্যাপ করার পর এই ঢাকনা মুখে পরিয়ে দিয়ে উপরে ফোঁটা ফোঁটা ক্লোরোফর্ম ঢালবেন, যা অপহৃতের নাকে ঢুকবে। তাতে ব্যাপারটা নিরাপদ থাকবে। কতটা দিতে হবে জানা নেই, ডোজ় বেশি হয়ে গেলে যদি ঘুমই না ভাঙে? বিজন জোগাড় করলেন pethidine ইঞ্জেকশন আর ক্লোরোফর্ম। পাঁচ, সম্ভাব্য শিকার খুঁজবে কে? টিউশনির ফাঁকে সময় বের করা মুশকিল বিজনের, খোঁজার ভার নিলেন দেবাশিস।
শিকারের সন্ধানে পরের সপ্তাহদুয়েক এসপ্ল্যানেড, নিউমার্কেট, পার্ক স্ট্রিট, বালিগঞ্জ, আলিপুরে দিনভর ঘুরে বেড়াতেন দেবাশিস। বড়লোকরা তো এসব জায়গাতেই থাকে অধিকাংশ। কিন্ত ওভাবে কি হয়? অনেক ঘুরেফিরেও সুবিধে হচ্ছিল না। টার্গেট চিহ্নিত করছেন হয়তো, কিন্তু আলাপ জমাতে পারছেন না। প্রায় হাল ছেড়ে দেওয়ার মুখে যখন, এক সন্ধ্যায় আচমকাই সন্ধান পেলেন সম্ভাব্য শিকারের।
২ অক্টোবর। বিকেল-সন্ধের মাঝামাঝি তখন। এসপ্ল্যানেড থেকে যতীন দাস পার্কের টিকিট কেটে দেবাশিস প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছেন। দেখলেন, একটু দূরেই দাঁড়িয়ে দুটি ছেলে | দু’জনেরই বয়স তেরো-চোদ্দো হবে। ধোপদুরস্ত জামাকাপড়। দেবাশিস কান পাতলেন। দু’জনেই সিনেমা আর সিরিয়ালের গল্পে মগ্ন। ট্রেন এল। দুই কিশোরের পিছুপিছুই ট্রেনে উঠলেন। বসলেন ওদের পাশেই। গল্প তখনও লাগাতার চলছে সিনেমার।
“পরবর্তী স্টেশন পার্ক স্ট্রিট, আগলা স্টেশন পার্ক স্ট্রিট, দ্য নেক্সট স্টেশন ইজ় পার্ক স্ট্রিট।” ঘোষণা হতেই উঠে দাঁড়াল দু’জন। উঠে পড়লেন দেবাশিসও, ওদের সঙ্গেই নামলেন পার্ক স্ট্রিটে। প্ল্যাটফর্মেই আলাপ জমালেন দেবাশিস।
—এক্সকিউজ় মি, তোমাদের সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?
—বলুন।
—আমি এইচ কে গুপ্ত। টিভি সিরিয়াল বানাই। একটু কথা বলতাম। তার আগে তোমাদের নামটা জানা দরকার।
—আমি অনুরাগ, অনুরাগ আগরওয়াল। আর ও সমীর প্যাটেল। সিরিয়ালের ব্যাপারে কী বলছিলেন…
—আসলে আমি একটা সিরিয়াল বানাচ্ছি। ‘সফেদ ধাগে’। একজন টিন-এজারের গল্প। অ্যাক্টর খুঁজছি, পাচ্ছি না। তোমাকে দেখে মনে হল, রোলটায় ভাল মানাবে। অবশ্য তুমি যদি রাজি থাকো, তবেই…
—কী বলছেন? আমরা রাজি, আর কে কে আছে সিরিয়ালে?
দেবাশিস বুঝতে পারেন, শিকার টোপ গিলেছে, এখন শুধু প্ল্যানমাফিক বঁড়শিতে গাঁথার অপেক্ষা।
—সব বলব, কিন্তু দু’জনকে তো নিতে পারব না। অনুরাগ এই ছবিটার জন্য পারফেক্ট। সমীর, তোমারটা পরের ছবিতে ভাবব। কিন্তু তোমার বাড়ির লোকজন রাজি হবেন তো অনুরাগ?
—হ্যাঁ হ্যাঁ, হবে। শুরুতে বলব না, সিরিয়াল টেলিকাস্টের আগে সারপ্রাইজ় দেব।
—আসলে শুটিংয়ে কী হয় জানো, টাইমের ঠিক থাকে না কোনও। যখন-তখন ‘কল টাইম’ থাকে। তোমার বাড়িতে অ্যালাও করবে কি?
—ও আমি ম্যানেজ করে নেব আঙ্কল। সিরিয়াল কবে থেকে দেখাবে টিভিতে?
দেবাশিস হাসেন, পিঠে হাত রাখেন অনুরাগের।
—হবে হবে। তোমার পুজোর ছুটির মধ্যেই শুটিং সেরে ফেলব। এখন বাড়ির কাউকে কিছু না বলাই ভাল।
—বলব না আঙ্কল, নিশ্চিন্তে থাকুন।
অনুরাগের বাড়ি কোথায়, কে কে আছেন, কে কী করেন, টেলিফোন নম্বর কী, সব কথার মাঝে খুঁটিয়ে জেনে নিলেন দেবাশিস। বললেন, ফোনে যোগাযোগ করবেন। সঙ্গে যোগ করলেন, বাড়ির অন্য কেউ ফোন ধরলে কিন্তু কেটে দেবেন। অনুরাগের গলা পেলে তবেই কথা বলবেন। না হলে বাড়ির লোক জেনে যাবে, আর জেনে গেলে অভিনয়ের অনুমতি না-ও দিতে পারেন। সকাল দশটা থেকে দুপুর সাড়ে বারোটার মধ্যে করবেন আঙ্কল, আমিই ধরব, আশ্বস্ত করল অনুরাগ|
সন্ধেবেলা বিজনের বাড়িতে বসে প্ল্যান হল, কাজটা পরের দিনই সেরে ফেলতে হবে। ৩ অক্টোবর বেলা এগারোটা নাগাদ রাসেল স্ট্রিটের পোস্ট অফিস থেকে ফোন গেল অনুরাগের বাড়ি। দুটো নাগাদ ময়দান স্টেশনে আসতে বলা হল অনুরাগকে, তড়িঘড়ি চলেও এল অভিনয়ের স্বপ্নে বিভোর কিশোর।
দেবাশিস বললেন, ‘তোমার ‘লুক টেস্ট’ হবে আজ, ক্যামেরাম্যানের বাড়ি যাই চল।’ নিয়ে গেলেন বিজনের বাড়ি, এদিক–ওদিক চক্কর কেটে ঘুরপথে, যাতে চট করে আবার কখনও চিনে আসতে না পারে। বিজনের পরিচয় দিলেন ক্যামেরাম্যান হিসাবে, নাম মিস্টার রায়।
‘সফেদ ধাগে’ সিরিয়ালের বানানো গল্প শোনানো হল অনুরাগকে। বিজন ক্যামেরা নিয়ে নানা পোজ়ে ছবি তুললেন কিশোরের। আসল ‘কাজ’টা কিন্তু দেবাশিস-বিজন করে উঠতে পারলেন না সেদিন। সাহসে কুলোল না। পৌনে পাঁচটা নাগাদ অনুরাগ বলল, দেরি হয়ে যাচ্ছে, মা-বাবা চিন্তা করবে এবার। দেবাশিস কালীঘাট স্টেশনে নিয়ে গিয়ে ময়দান স্টেশনের টিকিট কেটে দিলেন।
পরের সাক্ষাতের দিন ঠিক হল ফোনমারফত। ৪ অক্টোবর, কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে। দুপুর একটায়। ফের বিজনের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল অনুরাগকে। ঘটনাচক্রে সেদিন কোনও প্রতিবেশীর বাড়িতে সামাজিক অনুষ্ঠান, দিনভর আনাগোনা লোকজনের, হইচই | সেদিনও হল না, ফিরে গেল অনুরাগ, কিছু কাল্পনিক দৃশ্য অভিনয় করে দেখানোর পর।
সে-রাতে বিজন বললেন দেবাশিসকে, এভাবে ছেলেটাকে বারবার বাড়িতে আনা ঝুঁকির হয়ে যাচ্ছে। পাড়ার কিছু লোকজনের চোখে তো পড়ছেই। যা করার, খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে। আর দেরি করাটা মারাত্মক ঝুঁকি হয়ে যাবে।
ঠিক হল, ৬ তারিখ দুপুরে ফের ডাকা হবে অনুরাগকে। আর সেদিনই এসপার-ওসপার।
৬ অক্টোবর, দুপুর দেড়টা। কথা হয়েছিল ফোনে আগেই। অনুরাগকে নিয়ে দেবাশিস কসবায় পৌঁছতেই বিজন বললেন, ‘শুটিং শুরু পরের সপ্তাহে, আজকে তো ফাইনাল ‘লুক টেস্ট’। কিন্তু তোমার মুখটা তো একদম রোদে পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে। এতে তো চলবে না ভাই।’
অনুরাগ শুনেই ভীষণ মুষড়ে পড়ল। সাজানো চিত্রনাট্যে দেবাশিস-বিজনের পরের সংলাপ হল এরকম।
—মিস্টার রায়, চেহারায় ‘গ্লেজ়’ ফিরিয়ে আনার ওই ইঞ্জেকশনটা দিলে হয় না?
—মন্দ বলেননি, কিন্তু ঘুম পাবে তো একটু। অবশ্য ঘণ্টাখানেক মাত্র। তারপর উঠে পড়বে, মুখে ‘গ্লেজ়’ ফিরে আসবে। ফ্রেশ লাগবে অনেক।
অনুরাগ লাফিয়ে উঠল।
—দিন আঙ্কল, দিন। ইঞ্জেকশনটা দিন প্লিজ়।
Pethidine ইঞ্জেকশন দেওয়া হল। ডিসপোজ়েবল সিরিঞ্জ দেবাশিস কিনে রেখেছিলেন। ইঞ্জেকশন দেওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ কাটল | কিন্তু যাকে বলে ‘Deep Sleep’, তাতে তলিয়ে গেল না অনুরাগ। ঘুমঘুম আচ্ছন্ন ভাব, কিন্তু জেগে। ঘণ্টাখানেক পর উঠেই বসল অনুরাগ।
—আঙ্কল, ছবি তুলে নিন এবার।
ছবি তোলা হল। ততক্ষণে সন্ধে নেমেছে প্রায়। পাশের ফ্ল্যাটের ভাড়াটিয়াদের একজন পাড়ার কালীপুজোর ব্যাপারে কথাও বলতে এসেছেন। কাজ হাসিল সেদিনও হল না। অনুরাগকে মেট্রোতে ছেড়ে দিতে গেলেন দেবাশিস। রাসবিহারী মোড়ের PCO থেকে বাড়িতে মা-কে ফোন করল অনুরাগ, ‘একটু দেরি হচ্ছে। চিড়িয়াখানা গিয়েছিলাম। সমীরদের গাড়ির টায়ার পাংচার হয়ে গিয়েছিল। চিন্তা কোরো না। আধঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব।’
‘অপারেশন কিডন্যাপ’ বারবার তিনবার ফেল। সেই রাতে বিজন পরিষ্কার জানালেন দেবাশিসকে, তাঁর বাড়িতে আর সম্ভব নয়। ছেলেটাকে অনেকে দেখেছে, চিনে ফেলেছে। কৌতূহল বাড়ছে পাড়াপ্রতিবেশীর। কিডন্যাপের পর রাখার অন্য জায়গা খোঁজা দরকার।
হাওড়ার বালিতে দেবাশিসের এক পরিচিত ছিল। নাম পল্লব মুখার্জি ওরফে পলু। কাজকর্ম বলতে টুকটাক জমির দালালি, বাকি সময় এলাকায় দাদাগিরি। পরের দিনই বালি গিয়ে প্ল্যান খুলে বলা হল পলুকে। সব শুনেটুনে পলু বলল, ‘জায়গার ব্যবস্থা করে দিতে পারে ঘাসবাগানের অশোক রাই ওরফে ভোদা | তোমরা ১১ তারিখ এসো একবার, তার মধ্যে আমি কথা বলে রাখছি। হাওড়া স্টেশনের কফি কর্নারে বেলা এগারোটা নাগাদ দেখা হবে।’
১১ অক্টোবর। পলুর সঙ্গে কফি কর্নারে অপেক্ষা করছিল আর একটি ছেলে। এর নাম গোপাল, গোপাল সরকার | একে সঙ্গে রাখলে কাজের সুবিধে হবে— আলাপ করিয়ে দিল পলু | চারজনে মিলে ঘাসবাগানে যাওয়া হল ভোদার সঙ্গে দেখা করতে। বহু গলিঘুঁজি পেরিয়ে ভোদার বাড়ি। কথা হল। দেবাশিস-বিজন অল্পক্ষণেই বুঝলেন, ভোদা অপরাধের দুনিয়ায় জলের মাছের মতোই স্বচ্ছন্দ। হাওড়ার নটরাজ হোটেলের কাছে গম বিক্রি করে। এহ বাহ্য | আসলে এলাকার নামকরা মস্তান, দুর্দান্ত দাপট আছে |
টাকাপয়সার ভাগবাঁটোয়ারা নিয়ে কথা হল। কিডন্যাপের পর অপহৃতকে রাখার জায়গা দেখাতে নিয়ে চলল ভোদা। কাছেই একটি নুনের গোলা, বিশাল এলাকা জুড়ে | পরিত্যক্ত, নির্জন। অনেক ঘর, এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাওয়ার জন্য আঁকাবাঁকা গলিপথ | ভুলভুলাইয়ার সঙ্গে টক্করে জিততে না পারলেও লড়াই দেবে | ভোদা বিড়ি ধরিয়ে বলল, ‘এটাই ফিট জায়গা। কেউ টের পাবে না। রাতে কোনও পাহারা থাকে না। এখানে রাখতে গেলে তোমাদের দু’জনকেই পালা করে পাহারা দিতে হবে। আমার লোক পাহারা দেবে না।’
বিজন-দেবাশিস শত হলেও দাগি আসামি তো নন, একটু ঘাবড়ে গেলেন। বিজন বললেন, এই হানাবাড়িতে রাতভর একা পাহারা? অসম্ভব! দেবাশিস সায় দিলেন, অন্য জায়গা হলে ভাল হয়।
ভোদা ফ্রন্টফুটের প্লেয়ার। ব্যাকফুটের কোনও অস্তিত্বই নেই চিন্তাভাবনায় | হেসে আরেকটা বিড়ি ধরাল। বোঝা গেল, জায়গার অভাবটা কোনও সমস্যাই নয়। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সদলবলে পৌঁছল কাছেই Dikshit Transport Company-র গোডাউনে। কোম্পানি বন্ধ হয়ে গিয়েছে মাসছয়েক আগে। একজন দারোয়ান আছে, নাম ভগবতী| ভরদুপুরেই যার মুখ থেকে মদের গন্ধ ছিটকে বেরচ্ছে ভকভক| পাহারা দেওয়ার পাশাপাশি চোলাই মদ বেচা শুরু করেছে ইদানীং।
ভগবতী চাবি দিয়ে দিল এক কথায়। গুদামঘরটা বেশ বড়। নানা মাপের কাঠের প্যাকিং বক্স রাখা। বেশ পছন্দ হয়ে গেল দেবাশিস-বিজনের। হ্যাঁ, এটা চলবে।
এই সেই গুদামঘর
দু’জনে রওনা হয়ে গেলেন কলকাতায়। পরের দিন সকাল দশটায় অনুরাগের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে বলা হল দুপুর দেড়টা নাগাদ কালীঘাট মেট্রো স্টেশনে আসতে। দিনটা ১২ অক্টোবর। নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ি থেকে কাউকে না জানিয়ে বেরল অনুরাগ| ‘হিরো’ হওয়ার স্বপ্নে মাতোয়ারা কিশোর, দূরতম কল্পনাতেও ভাবেনি, আর ফেরা হবে না।
অনুরাগকে নিয়ে দু’জনে প্রথমে গেলেন চাঁদপাল ঘাট, তারপর লঞ্চে গঙ্গা পেরিয়ে হাওড়ায়। অনুরাগকে বললেন, হাওড়ায় একটা গোডাউনে শুটিং-এর লোকেশন। গোপাল ওপারের ঘাটে অপেক্ষা করছিল। দূর থেকে দেখেই রওনা হয়ে গেল পলু আর ভোদাকে খবর দিতে। বেলা তখন সাড়ে তিনটের কাছাকাছি।
দেবাশিস-বিজন যখন অনুরাগকে নিয়ে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির গুদামের রাস্তায়, গোপাল পথ আটকাল। দেবাশিসদের আলাদা ডেকে বলল, সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। দিনের আলোয় গোডাউনে ঢোকা যাবে না। লঞ্চঘাটে ফিরে অপেক্ষা করতে লাগলেন দেবাশিস-বিজন-গোপাল। এবং অনুরাগ। যে এতক্ষণে একটু অস্থির হয়ে পড়েছে, বলছে, বাড়িতে সন্ধের মধ্যে ফিরব বলে এসেছি। মা-বাবা খুব চিন্তা করবে। দেবাশিস আশ্বস্ত করলেন, টেকনিক্যাল সমস্যার জন্য দেরি হচ্ছে। কোনও চিন্তা নেই, তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব আমরা। মা-বাবাকে বুঝিয়ে বলব।
দিন তো গেল, সন্ধে হল | অনুরাগকে নিয়ে তিনজন ফের রওনা দিল গোডাউনে। পলু ও ভোদা ভিতরে অপেক্ষা করছিল। ঢুকেই ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল অনুরাগ। এ কোথায় এলাম? এখানে শুটিং হবে? ক্যামেরা কই, আলো কই, টেকনিশিয়ানরা কই? আর ওই দু’জন কারা? লুঙ্গি পরে বসে আছে, সামনে গ্লাস, বিশ্রী গন্ধ বেরচ্ছে মুখ থেকে? একটা প্যাকিং বক্স উঁচু করে রাখা একধারে। উপরে চট ও চাদর পাতা। একটা ছোট ল্যাম্প জ্বলছে টিমটিম। বিজনরা ঢুকতেই ভোদা দরজা বন্ধ করে দিল গোডাউনের, চাবি দিয়ে দিল ভিতর থেকে। দারোয়ান ভগবতী তখন বাইরে, চোলাইয়ের খদ্দেররা আসতে শুরু করেছে।
এই গুদামঘরে অনুরাগকে মারা হয়েছিল
ব্যাপারস্যাপার দেখে ভয় পেয়ে গেল অনুরাগ। কেঁদেই ফেলল দেবাশিসের হাত জড়িয়ে ধরে, ‘আঙ্কল, বাড়ি যাব | আমাকে প্লিজ় নিয়ে চলুন এখান থেকে। আমি অভিনয় করতে চাই না।’
দেবাশিস-বিজন তখন কিছুটা বিভ্রান্ত। ঠিক কীভাবে এগোবেন, বুঝতে পারছেন না। ভোদা ব্যাপারটা বুঝে দায়িত্ব নিয়ে নিল, এরপর চিল্লামিল্লি করবে, বেঁধে ফেল।
পাঁচজনে ঘিরে ধরে মুখে লিউকোপ্লাস্ট লাগিয়ে দেওয়া হল অনুরাগের, বেঁধে ফেলা হল হাত-পা। প্যাকিং বক্সের উপর শুইয়ে দিয়ে air purifier mask-এর মধ্যে কয়েক ফোঁটা ক্লোরোফর্ম দিয়ে নাকের কাছে ধরা হল। একটা ঝিমুনি ভাব এল ঠিকই, কিন্তু অচৈতন্য নয়।
সে-রাতে পাহারায় থাকল বিজন। ঠিক হল, ভোদা আর পলু রাতে মাঝেমাঝে এসে দেখে যাবে, কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না। দেবাশিস কলকাতায় চলে এলেন সে-রাতে। পরের দিন, ১৩ অক্টোবর, ফিরে এলেন সন্ধেবেলায়। বিজন বললেন, ‘কোনও কাজ হয়নি ক্লোরোফর্মে, সারারাত ছটফট করেছে অনুরাগ।’ সঙ্গে যোগ করলেন, ‘ফোন করেছ আগরওয়ালদের?’ দেবাশিস বললেন, ‘করব, কাল।’
বিজন এবার ফিরে গেলেন কলকাতায়। সে-রাতে পাহারার পালা দেবাশিসের। সন্ধেবেলা গুদামঘরে তখন গোপাল-পলু-ভোদা-দেবাশিস। ভোদা বখরার টাকার দাবি করল। এখনও জোগাড় হয়নি শুনে খেপে গিয়ে বলল, ‘এমন তো কথা ছিল না! আমি আগে টাকা না নিয়ে কোনও কাজে হাত দিই না। পলু বলেছিল বলে করেছিলাম। ২/৩ দিন ওয়েট করব, তার মধ্যে টাকা না পেলে…।’ কথা শেষ করল না ভোদা, কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে রক্ত হিম হয়ে গেল দেবাশিসের।
রাত বাড়ল। ভোদা একটা দোকানে নিয়ে গেল বাকি তিনজনকে। ডিনারে মশলা ধোসা, শেষ পাতে কুলফি। দেবাশিস পয়সা দিতে গেলেন, ভোদা থামিয়ে দিল, ‘আমার কাছে পয়সা চাওয়ার হিম্মত এ তল্লাটে কারও নেই। কেউ কথা বলে না আমার উপর।’
ফেরা হল গুদামে | তখন প্রবল ছটফট করছে অনুরাগ, কাঁদছে। মুখ বাঁধা থাকায় আওয়াজ বেরচ্ছে না, কিন্তু জল পড়েই চলেছে চোখ দিয়ে। পলু বলল, ‘ব্যাপারটা কিন্তু খারাপ দিকে যাচ্ছে। কলকাতার ছেলে, ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ে। টাকা যদি পেয়েও যাই, একে ছেড়ে দিলে সব বলে দেবে। মুখ তো চিনেই ফেলেছে। ধরা পড়লে লাইফ বরবাদ হয়ে যাবে।’
ভোদা সায় দিল, ‘সবার আগে দেবাশিস তোমরা ফাঁসবে। আনাড়ি মালের সঙ্গে কাজ করার এই মুশকিল। আমার জেলখাটা অভ্যেস আছে। ও ঠিক বেরিয়ে আসব কয়েক মাসের মধ্যে। তুমি আর বিজন সারা জীবনের মতো ভোগে।’
পলু বলল, ‘ভোদা ঠিক বলছে, একে বাঁচিয়ে রাখলে বিপদ।’
দেবাশিস এসব শুনে দিশেহারা তখন। অনুরাগের ছটফটানি, ভোদা-পলুর ভয় দেখানো, সব মিলিয়ে পাগল-পাগল অবস্থা। ঠিক, বাঁচিয়ে রেখে আর লাভ নেই, বলে দেবাশিসই প্রথমে চড়ে বসলেন অনুরাগের বুকের উপর। ঝাঁপিয়ে পড়ল বাকিরাও। গলায় গামছা দিয়ে ফাঁস দিল ভোদা, পা চেপে ধরল পলু-গোপাল। ছটফটানি থেমে গেল অনুরাগের, অল্প কিছু সময়ের মধ্যেই।
এবার? অনুরাগ বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সাদা স্ট্রাইপড শার্ট আর খয়েরি ট্রাউজ়ার পরে। পায়ে ছিল চটি। হাতে সোনার আংটি ছিল, গলায় সোনার চেন | সঙ্গে নিয়ে ছিল একটা ব্যাগ। যাতে ক্রিম রংয়ের শার্ট আর ট্রাউজ়ার ছিল, শুটিং-এ ইস্ত্রি করা ভাল জামাকাপড় পরবে, সম্ভবত এই ভেবেই। কালো সানগ্লাস ছিল, ছিল একটা ক্যামেরাও। হলুদ রঙের টুপি ছিল ব্যাগে, একটা খাতা-পেনসিলও নিয়েছিল। যদি ডায়লগ টুকে রাখতে হয়, এমনটাই ভেবে ছিল হয়তো। একটা মানিব্যাগ ছিল পকেটে, ভিতরে একটা কুড়ি টাকার নোট। আর ছিল একপাতা ভিটামিন ক্যাপসুল, যা দাদুর কথায় খেত রুটিন মাফিক।
যা পরে ছিল অনুরাগ, জ্বালিয়ে দেওয়া হল সব। ব্যাগের শার্টপ্যান্ট নিলেন দেবাশিস, পরের দিন রেখে এলেন বিজনের বাড়িতে| ক্যামেরাটাও দেবাশিসই নিয়েছিলেন, বেচে দিয়েছিলেন পরে। বিক্রির টাকা ভাগ করে নিয়েছিলেন পল্লব আর বিজনের সঙ্গে। গোপাল নিল সানগ্লাস। ওষুধের পাতাটা পল্লব রেখে দিল পকেটে।
ভোদাই ব্যবস্থা করল দেহ লোপাটের। বস্তায় অনুরাগের দেহ ভরে বেঁধে ফেলল দড়ি দিয়ে। রাত গভীর হলে সবাই রওনা হল গঙ্গার ঘাটে, গলির গলি তস্য গলি দিয়ে, নুনগোলার পাঁচিল টপকে। ভোদাই পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। অন্ধকারে হোঁচট খেয়ে পায়ে চোট লাগল দেবাশিসের।
বস্তাবন্দি দেহ নিয়ে পলু ও গোপাল গঙ্গায় নামল। সাঁতরে কিছু দূর গিয়ে ভাসিয়ে দিল জলে। সেদিন ছিল চতুর্থী। দেবীর বোধনের আগেই পুজোর মরশুমে গঙ্গায় ভাসান হয়ে গেল নিরপরাধ এক কিশোরের, যে অন্ধের মতো বিশ্বাস করেছিল দেবাশিস-বিজনকে।
পুলিশের কাছে তো বটেই, আদালতেও দেবাশিস–বিজন বারবার বলেছিলেন, অপহরণের পর হত্যার কোনও পরিকল্পনাই ছিল না তাঁদের। অনভিজ্ঞতা এবং ভয়ের যোগফলে ঘটে গিয়েছিল। কিন্তু অনুরাগ জীবিতই নেই আর, এটা জেনেও এরপর ওঁরা দু’জন যা করেছিলেন, ক্ষমাহীন।
১৪ অক্টোবর, লিখেছি আগে, প্রথম ফোন গিয়েছিল আগরওয়ালদের বাড়িতে। ১৫ অক্টোবর সন্ধে সাতটা কুড়িতে টাকা হাতবদল হল। পাঁচ টাকার বিনিময়ে একটি স্থানীয় বাচ্চা ছেলেকে শিখিয়ে-পড়িয়ে পাঠিয়ে দিলেন দু’জনে, বসুশ্রীর সামনে দাঁড় করানো গাড়ি থেকে টাকা নিতে। টাকা এল, ভাগাভাগি হল। এবং দু’জনে ঠিক করলেন, ভোদা-পলু-গোপালকে বলবেন, টাকা আদৌ পাওয়াই যায়নি। ওদের ভাগ দেওয়ার দরকার নেই। ভোদা-বাহিনী অবশ্য অত সহজে মেনে নেওয়ার পাত্র ছিল না। সরাসরি হুমকি দিল, ওসব গালগল্প শুনিয়ে লাভ নেই। কালীপুজোর মধ্যে টাকা না পেলে দেবাশিস-বিজনের লাশ খুঁজে পাওয়া যাবে না। অনুরাগের মতো দশা হবে।
ক্রমাগত হুমকিতে ভয়ই পেয়ে গেলেন দু’জন। ঠিক করলেন, আবার ফোন করবেন আগরওয়ালদের। ১৭ অক্টোবর থেকে ফোন করা শুরু হল। ততক্ষণে তদন্তে নেমে পড়েছে গোয়েন্দা দফতর। আগরওয়াল পরিবারও আঁচ পেয়ে গিয়েছে, বড়সড় গোলমাল আছে কোনও।
মোবাইল ফোন তখনও আসেনি এদেশে। এলে, এবং অভিযুক্তরা ব্যবহার করলে কিনারা করা অনেক সহজ হত। আগরওয়ালদের ল্যান্ডলাইনে আড়ি পাতা হল। ‘মিস্টার গুপ্তের’ ফোন তিন-চারদিন অন্তর আসতেই থাকল টাকার দাবি জানিয়ে। বক্তব্য, আশি হাজার পাইনি। কিন্তু আর আপনাদের বাড়ির ছেলেকে রাখতে চাই না। হাজার বিশেক দিলেই ছেড়ে দেব। দেবীলাল-শৈলেন্দ্র প্রতিবারই কথা বলতে চাইতেন অনুরাগের সঙ্গে। উলটোদিকের বাঁধাধরা উত্তর ছিল, টাকা পাওয়ার আগে কথা বলানো যাবে না। না পুলিশ, না আগরওয়াল পরিবার, কেউই তখনও জানে না, অনুরাগ আর বেঁচে নেই।
দাবি করা টাকার অঙ্ক কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কুড়ি থেকে নেমে এল পাঁচ হাজারে। পুলিশের পরামর্শ অনুযায়ী ফাঁদ পাতা হল। দেবীলাল জানালেন, তিনি রাজি। ফোনে নির্দেশ এল, ৩ নভেম্বর কালীঘাট মন্দিরের কাছে একটা ডাস্টবিনে কাগজের প্যাকেটে টাকাটা রেখে দিতে। ছেঁড়া কাগজে ভরতি প্যাকেট নিয়ে সকাল দশটায় ডাস্টবিনে প্যাকেট রেখে দিলেন শৈলেন্দ্র। সোয়া দশটায় দেবাশিস ডাস্টবিনের কাছাকাছি এলেন, তাকাচ্ছিলেন এদিক-ওদিক। সাদা পোশাকের পুলিশ কলার চেপে ধরল।
—আপনি মিস্টার গুপ্ত?
—না, মানে…
—অনুরাগ কোথায়?
—কে অনুরাগ?
একটি জোরদার থাপ্পড়ের প্রয়োজন হল, যা গালে পড়লে মিনিটতিনেক কানমাথা ভোঁ ভোঁ করার কথা। ওটুকুই যথেষ্ট ছিল।
—স্যার, আমি দেবাশিস ব্যানার্জি। অনুরাগকে মেরে ফেলেছি আমরা। আমি একা ছিলাম না।
বাকি যারা ছিল, বিজন-পল্লব-ভোদা-গোপাল, ধরা পড়ল কয়েকদিনের মধ্যেই। জেরায় সব স্বীকার করল অভিযুক্তরা। কিন্তু একটাই সমস্যা, অনুরাগের দেহ পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। দেহ না পেলে মৃত্যু প্রমাণ করা দুরূহ | অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসা করা হল, একই স্বীকারোক্তি কি আদালতে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত? সবার আগে রাজি হলেন দেবাশিস।
এখানে একটু আইনের ব্যাখ্যা জরুরি। তফাতটা বোঝানো জরুরি, পুলিশের কাছে করা স্বীকারোক্তি আর আদালতে বিচারকের এজলাসে করা স্বীকারোক্তির। গ্রেফতারের পর পুলিশ ধৃতের মৌখিক স্বীকারোক্তির বয়ান লিপিবদ্ধ করতে পারে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৬১ ধারায়। কিন্তু এই স্বীকারোক্তি প্রামাণ্য হিসেবে গ্রাহ্য নয় আদালতে, যতক্ষণ না তা অন্য সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়ে তর্কাতীতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে। পরিভাষায়, corroborative evidence, সহায়ক প্রমাণ মাত্র, স্বতঃসিদ্ধ নয়। হতেই পারে, মেরেধরে ভয় দেখিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করেছে পুলিশ। তাই এই আইনি রক্ষাকবচ।
আদালতে বিচারকের কাছে দেওয়া স্বীকারোক্তির (judicial confession, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৬৪ ধারা) প্রমাণমূল্য ঢের বেশি, এ প্রমাণমূল্য অকাট্য (substantive evidence), যদি সেটা হয় সত্যি এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। এবং যদি তার সাধারণ সমর্থন মেলে অন্য সাক্ষ্যপ্রমাণে, সে সরাসরিই (direct evidence) হোক বা পারিপার্শ্বিক (circumstantial), শাস্তি একরকম অনিবার্যই |
কী করে বোঝা যাবে, আদালতে স্বীকারোক্তি পুলিশের চাপে কি না? সে বিধানও আছে আইনে। প্রাক্-স্বীকারোক্তি পালনীয় নিয়ম রয়েছে। যা মানতে হয় বিচারককে। প্রথামাফিক, পুলিশ পেশ করে আর্জি। জানায়, আদালতে স্বীকারোক্তিতে রাজি হয়েছে অভিযুক্ত। আবেদন গৃহীত হলে দিন স্থির হয় স্বীকারোক্তির। আদালতে অভিযুক্ত হাজির হলে কিছু বাঁধাধরা প্রশ্ন করেন বিচারক। নমুনা দেওয়া যাক।
‘আপনি কি অমুক মামলায় দোষ স্বীকার করতে চান? করলে, কেন চান?
আমি ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশের লোক নই। আপনি কিন্তু আইনত দোষ স্বীকার করতে বাধ্য নন আসামি হিসেবে। তবু যদি স্বীকার করেন, বিচারপর্বে সেই স্বীকারোক্তি আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে। এটা জানেন তো?
পুলিশ কি আপনাকে বলেছে যে দোষ স্বীকার করলে মামলা থেকে অব্যাহতি পাবেন বা সাজা কম হবে?
আপনি কি পুলিশের নির্দেশে বা চাপে পড়ে দোষ স্বীকার করতে এসেছেন? নির্ভয়ে বলুন।
আপনি এই মামলায় পুলিশি হেফাজতে থাকাকালীন আপনার প্রতি কি কোনও দৈহিক বা মানসিক অত্যাচার হয়েছে? দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন থাকলে দেখাতে পারেন।
আপনি দোষ স্বীকারে বাধ্য নন, আবার বলছি। তবু যদি চান স্বীকার করতে, চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি আবার ভেবে দেখার। তারপরও যদি স্বীকারোক্তি দিতে চান, লিপিবদ্ধ করব।
দেখতেই পাচ্ছেন, এজলাসে পুলিশ নেই। অনুরোধ, যা বলবেন, সত্যি বলবেন এবং স্বেচ্ছায় বলবেন। যদি স্বীকারোক্তির ব্যাপারে মত পরিবর্তন করেন, জানাবেন কাল, চব্বিশ ঘণ্টা ভেবে দেখার পর। আপনার মতই গ্রাহ্য হবে।’
উপরে যা যা পড়লেন, সবই দেবাশিসকে জিজ্ঞাসা করলেন বিচারক। দেবাশিস অনড় থাকলেন স্বীকারোক্তিতে। “কেন দোষ স্বীকার করছেন”— এর উত্তরে যা বললেন, হুবহু তুলে দিচ্ছি।
—পরিস্থিতি এমন হয়ে গেছে যে আমি যা করেছি তাতে বাইরের জগতে সবাই আমাকে ঘৃণা করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি সাজা না পাই, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি কিছুতেই শান্তি পাব না। যখন আমাকে অ্যারেস্ট করে আমার বাড়ি নিয়ে যায়, তখন আমার মা বলেছিলেন, এর থেকে যদি মরার খবর শুনতাম তা হলে খুশি হতাম। আমি যা অন্যায় করেছি তার সাজা আমি পেতে চাই।
দেবাশিস শুধু নন, গোপাল এবং ভোদাও স্বীকারোক্তি দিল আদালতে।
তদন্তকারী অফিসার দুলালবাবু তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের কাজটা করলেন অসামান্য। ঘটনাপ্রবাহ নিখুঁত উঠে এল চার্জশিটে। বিরল মামলা, শুরুতে লিখেছি। অপহরণ এবং হত্যার কেস অনেক হয়েছে এদেশে। আলোচ্য মামলা বিরল, কারণ দেহই পাওয়া যায়নি খুন হওয়া অপহৃতের। পুলিশি পরিভাষায়, ‘corpus delicti’, অর্থাৎ ‘body of crime’-ই মেলেনি। লাতিন শব্দবন্ধ, সোজা বাংলায়, অপরাধ যে আদৌ ঘটেছে তার সুনির্দিষ্ট প্রমাণ। একজন নিখোঁজ হয়ে গেল এবং আর খুঁজে পাওয়া গেল না। দেহ না পাওয়া পর্যন্ত কী করে প্রমাণ হবে যে নিখোঁজ নিহত হয়েছে?
এই যুক্তিতেই তর্ক সাজালেন অভিযুক্তদের আইনজীবী।
‘Corpus Delicti’ ছাড়াই খুনের ঘটনা প্রমাণ এবং অপরাধীদের শাস্তিদানের নজির আছে অতীতে। খুব অল্পসংখ্যক মামলায়। তদন্তকারী অফিসারের পক্ষে কাজটা ছিল অসম্ভব কঠিন, অক্সিজেন মাস্ক ছাড়াই দুর্গম পাহাড়ে চড়ার মতোই। আদালতে দেবাশিস-ভোদা-গোপালের দেওয়া জবানবন্দি ছিল, কিন্তু শুধু তার ভিত্তিতে অপরাধীদের দোষী সাব্যস্ত করতে প্রয়োজন ছিল ওই জবানবন্দির প্রতিটি দাঁড়ি-কমা-সেমিকোলন পারিপার্শ্বিক প্রমাণের ( circumstantial evidence) মাধ্যমে নিখুঁত উপস্থাপনার। যাতে ঘটনার শুরু থেকে শেষ, ফাঁক না থাকে কোনও, বৃত্ত সম্পূর্ণ হয় তর্কাতীত।
অনুরাগের ব্যাগ থেকে যা যা নিয়েছিল যে যে, উদ্ধার হল সব। ঘটনার দিন হাওড়ার লঞ্চঘাটে দেবাশিস ও বিজন যে এক কিশোরকে নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন বেশ কিছুক্ষণ, তার সমর্থন পাওয়া গেল এক প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ানে। তিনজনের ছবি জেটির সমস্ত কর্মীদের বারবার দেখানোর পর। বস্তাবন্দি দেহ নিয়ে চারজন যখন গঙ্গার পথে সে-রাতে, মাঝরাস্তায় দেখে ফেলেছিলেন একটি স্থানীয় গ্যারেজের দুই কর্মী। যাঁরা গাড়ি সারাচ্ছিলেন ল্যাম্পপোস্টের আলোয়। যাঁদের কৌতূহলী দৃষ্টি নজরে পড়ায় ভোদা ধমকেছিল, ‘মুখ বাড়িয়ে দেখা বার করে দেব হারামজাদা! বেশি চালাক, না?’ সেই দুই কর্মী বয়ান দিলেন।
বয়ান দিলেন দারোয়ান ভগবতীও, ধরে আনা হল বিহারের বাড়ি থেকে| যাকে ঘটনার পর ভোদা বলেছিল, ‘তুনে বহুত কুছ দেখ লিয়া| ভাগ যা ইহাঁসে, নেহি তো খালাস কর দেঙ্গে।’
গুদামের ভিতর থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল বেশ কিছু পায়ের ছাপ, যার অধিকাংশই ‘ডেভেলপ’ করা যায়নি| কিছু অবশ্য ‘ডেভেলপ’ করা গিয়েছিল, যা মিলে গিয়েছিল দেবাশিসের পায়ের ছাপের সঙ্গে।
শনাক্তকরণ প্রক্রিয়াও চলল বিচারপর্বে, আইনের ভাষার ‘Test Identification Parade’। যাতে অংশ নিল অনুরাগের বন্ধু সমীর প্যাটেল, চিনিয়ে দিল মেট্রো স্টেশনে আলাপ হওয়া দেবাশিসকে। যে দোকানগুলি থেকে কেনা হয়েছিল লিউকোপ্লাস্ট, Pethidine এবং air purifier mask, তার কর্মচারীরাও শনাক্ত করলেন দেবাশিস-বিজনকে।
সিটি সেশনস কোর্টের বিচারক ৭৭ জন সাক্ষীর বয়ান নথিবদ্ধ করলেন। দেবাশিস-গোপাল-অশোকের আদালতে স্বীকারোক্তি এবং সমস্ত তথ্যপ্রমাণ বিবেচনা করে ’৯১-এর ১৪ ডিসেম্বর রায় দিলেন। পাঁচ অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা ঘোষণা হল যাবজ্জীবন কারাবাসের। আবেদন দাখিল হল হাইকোর্টে। শুনানি চলাকালীনই, এগারো বছর কারাবাসের পর নিম্ন আদালত থেকে জামিন পেয়েছিল বিজন বড়ুয়া বাদে বাকি চারজন। সে জামিন নাকচ করে দিল হাইকোর্ট। যাবজ্জীবন কারাবাসের রায় বহাল রেখে আদালতে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ জারি হল জামিনে মুক্ত চারজনের উপর।
রায়ে বিচারপতিরা লিখলেন, “We are of the considered view that prosecution successfully established a complete chain of circumstances from its oral and documentary evidence which taken as a whole unerringly established the guilt of each and every appellant.”
Robert Louis Stevenson তাঁর অন্যতম জনপ্রিয় উপন্যাস ‘Kidnapped’-এ লিখছেন, “I have seen wicked men and fools, a great many of both; and I believe they both get paid in the end; but fools first.” (দু’ধরনের লোকই দেখেছি আমি। শয়তান আর বোকা, দুই-ই দেখেছি অনেক| উভয়কেই মূল্য চোকাতে হয়। তবে আগে বোকাদের)|
ঠিকই। অপরাধীরা শয়তানের প্রতিরূপ তো ছিলই, না হলে তরতাজা এক কিশোরকে ওভাবে খুন করে ভাসিয়ে দেওয়া যায় গঙ্গাবক্ষে? তবে তার চেয়েও বেশি বোকা ছিলেন দেবাশিস-বিজন| যদি প্রথম বারের মুক্তিপণের টাকায় সন্তুষ্ট থাকতেন, আশি হাজার পাওয়ার পরও বেসামাল লোভে যদি আর ফোন না করতেন আগরওয়াল পরিবারে, ধরা পড়ার সম্ভাবনা ছিল শূন্য। কে ধরত, কীভাবে ধরত, সূত্র পেত কোথায়? খুনের চিত্রনাট্য-সংলাপ-পরিচালনা অজানাই থেকে যেত, পুলিশও একটা সময় উৎসাহ হারিয়ে ফেলত কূলকিনারা না পেয়ে, অদৃষ্টকে শাপশাপান্ত করা ছাড়া আর কী-ই বা করার থাকত অনুরাগের আত্মীয়-পরিজনের, আর দিব্যি ঘুরে বেড়াত খুনিরা। নিরাপদে, নিরুপদ্রবে।
এমনই হয়। কখনও অতিচালাকি, কখনও অতিলোভ কাল হয়ে দাঁড়ায় অপরাধীর।
ধর্মের কল। বাতাসে তো নড়বেই।
১.০৬ করুণাধারায় এসো
[নওলাখা হত্যামামলা
তদন্তকারী অফিসার সুজিত মিত্র]
এমন তো হওয়ার কথা নয়, আগে কখনও হয়নি!
সকাল সাড়ে আটটা হবে তখন। রোজকার মতো প্রতিবেশী দম্পতির ফ্ল্যাটের বেল বাজালেন মিস্টার খেতওয়াত। অন্যদিন একবার বাজালেই হয় মিস্টার নওলাখা দরজা খুলে দেন, নয় মিসেস নওলাখা। সকালের চা-বিস্কুট প্রায় রোজই নওলাখা পরিবারের সঙ্গেই খান যুগলকিশোর খেতওয়াত। বছরভর একই রুটিন। এদিন হঠাৎ অন্যথা, টানা বেল বাজিয়ে গেলেও কোনও সাড়াশব্দ নেই কেন? কী এমন হল? শরীর খারাপ? যদি হয়-ও, একসঙ্গে দু’জনের? নাহ, গোলমাল লাগছে।
সাধারণত পৌনে ন’টা থেকে ন’টার মধ্যে রোজকার গৃহকর্মীরা চলে আসেন নওলাখা-দম্পতির ফ্ল্যাটে। সবার আগে আসেন প্রতিমা। দীর্ঘদিন কাজ করছেন এ বাড়িতে, খুবই বিশ্বাসী। ফ্ল্যাটের একটি ডুপ্লিকেট চাবিও তাঁর কাছে রাখা থাকে, কখনও যদি মালিক-মালকিনের অনুপস্থিতিতে জরুরি প্রয়োজন হয় ঘর খোলার।
প্রতিমা এলেন, দরজার বাইরেই অপেক্ষা করছিলেন উদ্বিগ্ন মিস্টার খেতওয়াত। আর এক প্রস্থ বেল বাজানোতেও যখন দরজা খুলল না, ব্যবহার করা হল ডুপ্লিকেট চাবি। ভিতরের দৃশ্য মর্মান্তিক, বীভৎসও বলা চলে। পুলিশে খবর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে মিনিটখানেকও লাগল না অন্য আবাসিকদের।
ভবানীপুর থানার ঘটনা, প্রায় ছাব্বিশ বছর আগে। কেস নম্বর ৫৬৩, তারিখ ২৫/১২ /৯১, ধারা ১২০ বি/ ৩০২/ ৩৯৪ /৩৪ আইপিসি। অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, খুন, লুঠ করতে গিয়ে ইচ্ছাকৃত কাউকে আঘাত করা এবং একই অপরাধের উদ্দেশ্যে একাধিকের সম্মিলিত পরিকল্পনা।
শরৎ বোস রোডের উপর এগারো তলার অভিজাত বহুতল ‘রামেশ্বর অ্যাপার্টমেন্টস’। সেন্ট জনস ডায়াসেশন স্কুলের লাগোয়াই প্রায়। দশতলায় ফ্ল্যাট নম্বর ১০সি-তে থাকতেন নওলাখা-দম্পতি। যাঁদের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হল দরজা খোলার পর। প্রশস্ত ফ্ল্যাট, ঢুকেই একটা বড় হলঘর। দুটো বেডরুম, অ্যাটাচড বাথ সহ। একটা গেস্টরুম। রান্নাঘর যেমন থাকে তেমন। হলঘরের একটা দিক ডাইনিং রুম হিসেবে ব্যবহার হত। আর এক কোণায় ছোট্ট একফালি জায়গায় পার্টিশন করে লাইব্রেরি-কাম-স্টাডিরুম। সম্পন্ন পরিবারে যেমন হয়, ফ্ল্যাট জুড়ে দামি আসবাবপত্র সাজানো-গোছানো পরিপাটি।
গিরিশকুমার নওলাখার (৫৯) নিথর দেহ পড়ে আছে স্টাডিরুমের কার্পেটের উপর। পাজামা-পাঞ্জাবি শরীরে। গলায় একটি দামি শাল দিয়ে ফাঁস দেওয়া। নাকমুখ দিয়ে চুঁইয়ে পড়েছে রক্তবিন্দু। সন্দেহ নেই কোনও, শ্বাসরোধ করে খুন। একজোড়া পুরনো ফুটিফাটা চপ্পল, যা দৃশ্যতই গিরিশবাবুর হতে পারে না, পড়ে আছে মৃতদেহের পাশে। একটু দূরে একটি খালি গ্লাস।
বীণা নওলাখার (৫৫) প্রাণহীন দেহ দুটি বেডরুমের একটিতে, পড়ে আছেন উপুড় হয়ে। প্রায় বিবস্ত্রা, রাতপোশাকটি ছিন্নভিন্ন। চোখেমুখে আঘাতের চিহ্ন, রক্তপাতও হয়েছে একটু। পেটের নীচে একটি বালিশ। গলায় শাড়ি দিয়ে ফাঁস দেওয়ার চেষ্টা করেছে আততায়ী বা আততায়ীরা। শাড়ির একটি প্রান্ত গলায় জড়ানো, অন্যপ্রান্ত বাঁধা সিলিংফ্যানে। মৃতার হাউসকোট ভাসছে লাগোয়া বাথরুমের কমোডে। হলঘরের টেলিফোন এবং ইন্টারকম সংযোগ-বিচ্ছিন্ন, তার কেটে দিয়েছে যে বা যারা ঢুকেছিল।
রামেশ্বর অ্যাপার্টমেন্ট
এক পুত্র এবং এক কন্যা ছিল নওলাখা-দম্পতির। কন্যা থাকেন ইন্দোরের শ্বশুরবাড়িতে। পুত্র নীলেশ আর পুত্রবধূ অনুরাধা ১১ ডিসেম্বর বেড়াতে গিয়েছিলেন উত্তর ভারতে। ফেরার কথা ছিল ২৪ তারিখ। ফোন করে দিনদুয়েক আগে মা-বাবাকে জানিয়েছিলেন, প্লেনের টিকিট না পাওয়ায় ২৬ তারিখ ফিরবেন। সস্ত্রীক নীলেশ যে ঘরটিতে থাকতেন, সেটি অক্ষত, তালাবন্ধ।
বাকি ঘরগুলি অবশ্য অক্ষত ছিল না। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আসবাবপত্র। ভেঙে তছনছ করা হয়েছে গেস্টরুমের কাঠের আলমারিটি। ইতস্তত পড়ে আছে কাঠের টুকরোটাকরা। বেশ কিছু জিনিসপত্র যে লুঠ হয়েছে, অনায়াসে অনুমেয়।
কেসের তারিখটি শুরুতে লিখেছি, খেয়াল করবেন। ২৫/১২/ ৯১। বড়দিনের সকাল। ক্রিসমাস ইভের নিশিযাপন শেষে একটু দেরি করে ঘুম ভাঙছে কলকাতার। রাস্তাঘাটে মানুষজন, গাড়িঘোড়া কম। দেরি আছে ভিক্টোরিয়া-চিড়িয়াখানা-পার্ক স্ট্রিটে-রেস্তোরাঁ-ক্লাবে জনপ্লাবন শুরু হতে।
দম্পতি-হত্যার জেরে শুভদিনের সকাল অশুভ হয়ে দেখা দিল কলকাতা পুলিশের কাছে। প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন তৎকালীন নগরপাল, খবর পেয়ে দ্রুত এলেন ঘটনাস্থলে। এলেন ডিসি ডিডি (গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান)। ভবানীপুর থানার পুলিশ এবং গোয়েন্দা বিভাগের হোমিসাইড শাখার অফিসারেরা ততক্ষণে পৌঁছে গিয়েছেন। লালবাজার কন্ট্রোল রুম খবর পাওয়া মাত্র সংশ্লিষ্ট সবাইকে বার্তা দিয়েছে দ্রুত, “couple found murdered in Sarat Bose Road apartment, reach the spot at the earliest.”
কৌতূহলী জনতার লাগামছাড়া ভিড় তখন অ্যাপার্টমেন্টের বাইরে, সামাল দিতে গলদঘর্ম পুলিশ। জটিল কেসে যা সচরাচর হয় কলকাতা পুলিশে, প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে স্থানীয় থানার পুলিশ। গুরুত্ব বুঝে কখনও রহস্যভেদের দায়িত্ব দেওয়া হয় গোয়েন্দা বিভাগকে, কখনও থানার অফিসাররাই তদন্ত চালান। নগরপাল অকুস্থলে দাঁড়িয়েই সিদ্ধান্ত নিলেন, এই জোড়া খুনের তদন্ত করবে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট। হোমিসাইড শাখার তৎকালীন সাব-ইনস্পেকটর সুজিত মিত্র তদন্তকারী অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হলেন।
গিরিশবাবুর দেহের পাশে পড়ে থাকা চপ্পল আর গ্লাস, বীণাদেবীর হাউসকোট, ভাঙা আলমারির কাঠের টুকরো এবং ঘটনাস্থলের ডাইনে-বাঁয়ে-সামনে-পিছনের আদ্যোপান্ত খানাতল্লাশি করে তৈরি হল বাজেয়াপ্ত সামগ্রীর নথি। পুলিশি পরিভাষায় ‘seizure list’। মোটামুটি ‘ডেভেলপ’ করার যোগ্য হাতের আর পায়ের ছাপ পাওয়া গেল কিছু, বিভিন্ন মাপের। সংগ্রহ করা হল সযত্নে। লুঠ এবং জোড়া খুনে যে একাধিক ব্যক্তি জড়িত, সেই ধারণা বদ্ধমূল হল গোয়েন্দাদের। খুনি কে বা কারা, সে-সূত্র অবশ্য তখন পর্যন্ত অধরাই।
এখানে ‘রামেশ্বর অ্যাপার্টমেন্টস’-এর একটু বিবরণ প্রয়োজন। ১৯এ, শরৎ বোস রোডের বহুতলটি তৈরি করেছিলেন যুগলকিশোর খেতওয়াত সাতের দশকের শেষাশেষি। খেতওয়াত পরিবারের নানাবিধ ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড ছিল, তবে গৃহনির্মাণ আর পরিবহণ-ব্যবসাই প্রধান। নিজে সপরিবারে থাকতেন ডুপ্লে ফ্ল্যাটে, দশতলার ১০এ আর এগারোতলার ১১এ মিলিয়ে। একতলায় যুগলকিশোর আর তাঁর ভাই প্রহ্লাদের আলাদা দুটি অফিস ছিল। যথাক্রমে রামেশ্বর ট্রান্সপোর্ট লিমিটেড এবং ভারত রোডওয়েজ় লিমিটেড। আর ছিল রিসেপশন সেন্টার, কেয়ারটেকারের অফিস এবং একটি কমিউনিটি হল। দুই থেকে দশ, অন্য প্রতিটি তলায় চারটি করে আবাসিক ফ্ল্যাট।
আবাসিকরা সকলেই অর্থবান ছিলেন, সুরক্ষা-সতর্কতায় কার্পণ্য করেননি একটুও। উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা প্রাঙ্গণ, লোহার সূচিমুখ শলাকা পাঁচিল বরাবর। দুটি গেট বাইরে। একটি ঢোকার, অন্যটি বেরনোর। ভিতরেও মজবুত নিরাপত্তা। দুটি সিঁড়ি, একটি আবাসিকরা ব্যবহার করেন, অন্যটি ফ্ল্যাটগুলির স্থায়ী বা অস্থায়ী কাজের লোক, সাফাইকর্মী, ড্রাইভার, দুধওয়ালা, খবরের কাগজ দেওয়ার লোক ইত্যাদি। দুটি স্বয়ংক্রিয় লিফট, সেখানেও একই নিয়ম। আবাসিকদের জন্য একটি, বাকিদের অন্যটি।
সুরক্ষা নিশ্ছিদ্র করতে বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন আবাসিকরা। National Security and Detective Agency-র উর্দিধারী রক্ষীরা তিন শিফটে পাহারায় থাকতেন চব্বিশ ঘণ্টা। ঢোকা-বেরনোর গেটে তো বটেই, বেসমেন্টের পার্কিং স্পেসে এবং একতলার রিসেপশনে সতর্ক প্রহরা ছিল। ইন্টারকমে রিসেপশনের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ছিল প্রতিটি ফ্ল্যাটের।
নিয়ম ছিল, পরিচিত আবাসিক বা কর্মী অ্যাপার্টমেন্টের সিঁড়ি বা লিফটে উঠলে নিরাপত্তারক্ষীরা কোনওরকম বাধা দেবেন না। পরিচিতের সঙ্গে অপরিচিত কেউ থাকলেও নয়। সম্পূর্ণ অপরিচিত কেউ ঢুকলে আটকানো হবে রিসেপশনে। নাম কী, কোন ফ্ল্যাটে যেতে চান, কী প্রয়োজন ইত্যাদি জেনে ইন্টারকমে যোগাযোগ করা হবে সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাটে। সবুজ সংকেত পেলে তবেই লিফট বা সিঁড়িতে ওঠার অনুমতি মিলবে। প্রতিটি ফ্ল্যাটে ছিল ইয়েল লক, আইহোল আর কলিং বেল।
এত কিছু, তবু খুন হয়ে গেলেন নওলাখা-দম্পতি! আজকের নিরিখে ভাবলে মনে হয়, সবই ছিল, শুধু সিসিটিভি-র ব্যবস্থাটা যদি থাকত! এখন শুধু অভিজাত এলাকায় বা ঝাঁ-চকচকে শপিং মলেই নয়, সিসিটিভি লাগানোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ছোট-বড় অসংখ্য আবাসনে ক্যামেরা লাগিয়েছেন নিরাপত্তা-সচেতন শহরবাসী। এতে অপরাধীকে চিহ্নিত করতে সুবিধে হয় আমাদের, ক্যামেরা আছে আন্দাজ করতে পারলে অবচেতনে একটা ভয়ও কাজ করে দুষ্কৃতীদের। এই সুবিধেটা থাকলে আলোচ্য জোড়া খুনের কিনারা নিশ্চিত সহজতর হত, মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হত না গোয়েন্দাদের।
মাথার ঘাম পায়ে ফেলার পর্বে ঢোকার আগে বলে নেওয়া ভাল, দু’তলা থেকে দশতলা, স্থায়ী গৃহকর্মীদের জন্য কোয়ার্টার ছিল প্রতি ফ্লোরেই। দশতলায় চারটি ফ্ল্যাটে ১০সি-র নওলাখা পরিবার ছাড়া থাকতেন ১০এ-তে খেতওয়াতরা, ১০বি আর ১০ডি-তে যথাক্রমে রাজেশ মেহতা আর দীপক মোঘানির পরিবার। নওলাখাদের তিনজন স্থায়ী কাজের লোক ছিলেন। প্রতিমা, যাঁর কথা শুরুতে বলেছি, মনিকা এবং শম্ভু। তিনজনই নির্দিষ্ট কোয়ার্টারে থাকতেন দশতলাতেই।
ময়নাতদন্ত সাঙ্গ হল বড়দিনের বিকেলেই। শ্বাসরোধ করেই খুন। দম্পতির মৃত্যুর আনুমানিক সময় রাত ১০টা থেকে সাড়ে ১০টার মধ্যে।
জিজ্ঞাসাবাদ দিয়ে শুরু হল তদন্ত। গিরিশবাবু বা বীণাদেবী, যে-ই দরজা খুলে থাকুন, পরিচিত না হলে নিশ্চয়ই খুলতেন না। আইহোলে দেখেছেন চেনা মুখ, অতএব খুলেছেন। সে বাসিন্দাই হন বা কর্মী, আবাসিকের কারও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভূমিকা অবশ্যম্ভাবী অপরাধের নেপথ্যে। পুলিশি পরিভাষায় যাকে বলে ‘insider job’। ৩৬টি ফ্ল্যাটের বাসিন্দা, যাঁরা সে-রাত্রে ছিলেন বা ছিলেন না, সমস্ত স্থায়ী-অস্থায়ী গৃহকর্মী, বেসরকারি নিরাপত্তা সংস্থাটির লোকজন, জেরা থেকে বাদ গেলেন না কেউ। চলল বড়দিনের রাতভর, তার পরের দিনও লাগাতার। কিন্তু বিধি বাম, শত চেষ্টাতেও ভরসাযোগ্য সূত্র মিলল না। কেউ স্বীকার করলেন না কিছু, এগোনোর মতো খড়কুটোও এল না হাতে। কেউ না কেউ মিথ্যে বা অর্ধসত্য বলছিলেন, এটা আন্দাজ করা যাচ্ছিল। কিন্তু প্রমাণহীন আন্দাজ খুনের তদন্তে মূল্যহীন।
প্রায় ৪৮ ঘণ্টা পেরিয়ে গেল ঘটনার, অন্ধকারে ঢিল ছোড়াতেই তখনও আটকে আছে তদন্ত। পুলিশি ব্যর্থতা নিয়ে মিডিয়ায় চলতে থাকল কাটাছেঁড়া, যেমনটা হয়ে থাকে। পুলিশ পি সি সরকার নয়, জাদুদণ্ড নেই কোনও রাতারাতি কিনারার, সেটা ভুলে গিয়েই।
বর্তমান সময়ে তদন্তের একটা সুবিধে আছে। প্রযুক্তির সুবিধে, ‘electronic surveillance’ -এর সুবিধে। মোবাইল ফোনের সূত্রে অনেক অপরাধের কিনারা হয়, সকলেই জানেন। দুর্ভাগ্য, ঘটনা ১৯৯১-এর, এদেশে মোবাইল ফোনের ব্যবহার শুরু যার চার বছর পর।
‘যেটা ছিল না ছিল না, সেটা না পাওয়াই থাক’ ধরে নিয়েই সে-সময়ে এগোতে হত গোয়েন্দাদের। কত যে অপরাধের কিনারা হয়েছে স্রেফ নিবিড় ‘সোর্সওয়ার্ক’ দিয়ে আট আর নয়ের দশকে, তালিকা শেষ করা যাবে না লিখে।
সোর্স বড় বিষম বস্তু পুলিশি দুনিয়ায়। ঠিকঠাক ব্যবহার করতে পারলে নব্বই শতাংশ ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ অবধারিত, না পারলে লবডঙ্কা। অপরাধ জগতের খবর কোনও সাধু-সন্ন্যাসী দেবেন না, দেবে অপরাধীরাই, যাদের নিত্য বিচরণ অন্ধকার জগতের অভ্যন্তরে। লালমোহনবাবুকে মনে পড়ছে লিখতে গিয়ে। প্রদোষচন্দ্র মিত্রের উদ্দেশে বলেছিলেন, “আপনাকে তো কাল্টিভেট করতে হচ্ছে মশাই।” সোর্স অবশ্য শুধু ‘কাল্টিভেট’ করলেই হয় না, ‘নার্চার’-ও করতে হয়। সোর্স লালন করাটাও এক বিশেষ শৈলী, সবাই পারেন না। যাঁরা পারেন, রহস্যভেদে তাঁরা এগিয়ে থাকেন। কিছু সতর্কতাও নিতে হয় সোর্স ব্যবহারে। সোর্সের মধ্যেই ভূত যাতে তৈরি না হয়ে যায়, সেটা খেয়াল রাখতে হয়। সোর্স আদৌ খাটাখাটনি করছে কি না, অফিসারের মন রাখতে গাঁজাখুরি গল্প শোনাচ্ছে কি না, নজরে রাখতে হয় তা-ও। কখনও কখনও সোর্সের পিছনে লাগানো হয় দ্বিতীয় সোর্স!
সত্যিটা স্বীকার করা যাক, গল্পের ফেলুদা-ব্যোমকেশ-এরকুল পোয়ারো-শার্লক হোমসের রহস্যভেদের রোমাঞ্চ-রোম্যান্স বাস্তবের তদন্তে থাকে কদাচিৎ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঘটনাস্থলে আধপোড়া সিগারেটের টুকরো থাকে না, থাকে না বাগানের ঝোপঝাড়ের কাদায় পায়ের ছাপ, থাকে না হুমকি-চিরকুট বা সমগোত্রীয় কিছু। সূত্র কিছুতেই না মিললে ভরসা করতে হয় সোর্সের উপর। কল্পনার গোয়েন্দা গল্প খুবই উপভোগ্য, গোগ্রাসে গেলার মতো। বাস্তবের তদন্ত কিন্তু ভিন্ন, অন্তত নব্বই শতাংশ ক্ষেত্রে। প্রতি পদে উত্তেজনার আঁচ পোহানো নেই, নির্মোহ পরিশ্রম আছে। রুদ্ধশ্বাস রোমাঞ্চ নেই, আপ্রাণ অধ্যবসায় আছে। আপন মনের মাধুরী নেই, মরিয়া একাগ্রতা আছে। নির্মাণের জগৎ মূলত, সৃষ্টির নয় ততটা।
তদন্তে ফিরি। সোর্স লাগানো হল একাধিক, প্রত্যেকে পোড়খাওয়া। বলে দেওয়া হল দুটো কথা। এক, জোড়া খুন নিয়ে অপরাধ-জগতে কিছু কানাকানি হচ্ছে কি না, খবর চাই। দুই, খোঁজখবর দরকার। অন্ধকার দুনিয়ার হোক বা না-হোক, আশেপাশের মহল্লায় কেউ কি হঠাৎ বেশি টাকা খরচ করছে? জীবনযাত্রায় চোখে পড়ার মতো বদল এসেছে কারও? মোদ্দা কথা, ‘যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই। পাইলে পাইতে পারো অমূল্য রতন’। এবং দ্রুত পাওয়াও গেল বহুপ্রতীক্ষিত সূত্র। সৌজন্য, তদন্তকারী অফিসারের দুর্ধর্ষ সোর্স নেটওয়ার্ক। খবর এল ২৭ তারিখ গভীর রাত্রে।
পদ্মপুকুরের কাছাকাছি এক ঠেকে মদ-জুয়ার আসর চলছে। যেখানে জাঁকিয়ে বসেছে ‘সোর্স’। এই ঠেকে তার দীর্ঘদিনের যাতায়াত। এসব আড্ডায় মোটামুটি সবাই সবার পরিচিতই হয় সচরাচর। সে-রাতের মোচ্ছবে মধ্যমণি এক অপরিচিত যুবক, জুয়ার বোর্ডে টাকা ওড়াচ্ছে দেদার। নতুন কেনা দামি ইয়াশিকা ইলেকট্রো-৩৫ ক্যামেরা দেখাচ্ছে বাকিদের। কিনে এনেছে বিলিতি মদের বোতল, ফুর্তির প্রাণ গড়ের মাঠ। নেশা চড়তেই জড়ানো গলায় হিন্দি গান, ঘুরেফিরে একটাই বারবার, “তদবির সে বিগড়ি হুয়ি তকদির বানা লে, তকদির বানা লে/ আপনে পে ভরোসা হ্যায় তো ইয়ে দাঁও লাগা লে, লাগা লে দাঁও লাগা লে…”। ১৯৫১-য় মুক্তিপ্রাপ্ত গুরু দত্ত পরিচালিত সুপারহিট ছবি ‘বাজি’-র সেই সুপারহিট গান। শচীন দেববর্মণের সুরে গীতা বালির লিপে গীতা দত্তের সেই আশ্চর্য জাদুকরী কণ্ঠে।
গানে অবশ্য সোর্সের মন ছিল না, রুচিও না। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ততক্ষণে সজাগ, এই চ্যাংড়া-টাইপ ছেলেটা এত টাকা পেল কী করে? আর এক পেগ বানানোর মাঝে নেহাতই হালকা চালে প্রশ্ন ছুড়ে দিল অপরিচিত যুবককে, ‘এখানে নতুন দেখছি, কী কাজ করো গুরু তুমি?’ যুবক ততক্ষণে নিরাপদ রকমের মাতাল, উত্তরও দিল হালকা চালেই, ‘পিয়নের কাজ করি বড়লোকের বাড়ি, ও কাজ আর করব না শালা!’
সোর্স-মারফত খবর পেয়ে সেই রাতেই তোলা হল ‘বড়লোকের বাড়ির পিয়নকে’। অপরাধ-জগতে কথিত আছে, লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগের ইন্টারোগেশন রুমে ঢুকলে সমস্ত রকম নেশা নিমেষে কেটে যায়। আকণ্ঠ মদ্যপান করে এলেও সংবিৎ ফিরতে সময় লাগে না বিশেষ। নতুন অতিথির ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হল না। ‘আদরযত্ন’ করার আগেই স্বীকারোক্তি এল স্বতঃস্ফূর্ত, ‘স্যার, আমি খোকন গিরি, খেতওয়াত সাহেবের অফিসে পিয়নের কাজ করি। খুন আমি একা করিনি। রাজু, কামিনী আর জগদীশও ছিল স্যার।’
—বেশ, পুরোটা বল এবার, কীভাবে করলি, কেন করলি?
উত্তরে খোকনের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া মুহূর্তের জন্য বাক্রুদ্ধ করে দিল দুঁদে গোয়েন্দাদেরও,
—লোভে পড়ে করেছি, খুন করার জন্য ম্যাডাম এক লাখ টাকা দেবেন বলেছিলেন।
—ম্যাডাম!! কোন ম্যাডাম?
—বিমলা ম্যাডাম, খেতওয়াত সাহেবের স্ত্রী।
বিস্ময়ের ধাক্কা কাটিয়ে উঠে জেরা শুরু হল খোকনকে। জানা গেল, যা ঘটেছিল, যেভাবে ঘটেছিল, যে কারণে ঘটেছিল।
খেতওয়াত পরিবার ও নওলাখা পরিবারের সামাজিক পরিচয় আটের দশকের শুরু থেকেই। নওলাখারা তখন থাকতেন বালিগঞ্জের মুলেন স্ট্রিটে। একসঙ্গে বাইরে খাওয়াদাওয়া, উৎসব-উদ্যাপন, ঘনিষ্ঠতা বেড়েছিল ক্রমশ। বিমলা খেতওয়াত এসব পছন্দ করতেন না। অন্তর্মুখী স্বভাবের মহিলা ছিলেন, একটু রক্ষণশীল মানসিকতারও। পুজো-আর্চা ঘর-সংসারেই বেশি স্বচ্ছন্দ। নওলাখা-দম্পতি আবার জীবনকে পূর্ণ মাত্রায় উপভোগে বিশ্বাসী, ক্লাব-পার্টিতে যাতায়াত নিয়মিত। যুগলকিশোর খেতওয়াতও তা-ই, হইহুল্লোড় তাঁরও মনপসন্দ।
নিয়মিত সামাজিক মেলামেশা চলতে চলতেই যুগলকিশোর আকৃষ্ট হলেন বীণা নওলাখার প্রতি। একতরফা ছিল না আকর্ষণ, বিবাহ-বহিৰ্ভূত প্রণয়ে সম্মতি ছিল বীণারও। দু’জনেই তখন মধ্যচল্লিশ। বালিগঞ্জের বাড়ি বেচে ১৯৮৬-তে রামেশ্বর অ্যাপার্টমেন্টে উঠে এলেন নওলাখারা। প্রণয়িনীকে প্রতিবেশিনী হিসেবে পাওয়ার তাগিদে জলের দরে দশতলার ফ্ল্যাটটি বেচলেন যুগলকিশোর। গিরিশ-বীণা দু’জনেই বেসরকারি সংস্থার উচ্চপদস্থ চাকুরে ছিলেন। স্বচ্ছলতা ছিল, কিন্তু ওই বহুতলে ফ্ল্যাট কেনাটা ছিল সামর্থ্যের বাইরে। গিরিশ নির্বোধ ছিলেন না, কেন সস্তায় ফ্ল্যাট দিচ্ছেন খেতওয়াত সাহেব, বিলক্ষণ বুঝেছিলেন। সম্ভবত পারিবারিক শান্তির কারণেই সব জেনেও মেনে নিয়েছিলেন, মানিয়েও নিয়েছিলেন।
মেনে নিতে পারেননি বিমলা খেতওয়াত, মানিয়ে নিতেও না। পরকীয়া থেকে স্বামীকে দূরে সরিয়ে আনতে চেষ্টার কসুর করেননি। ঝগড়া করেছেন স্বামীর সঙ্গে, প্রবল অশান্তি হয়েছে দিনের পর দিন, ঘরে ওঝা ডাকিয়ে তন্ত্রমন্ত্রেরও শরণ নিয়েছেন মরিয়া হয়ে। লাভ হয়নি কোনও। যুগলকিশোরের ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ বেড়েছে মিসেস নওলাখার সঙ্গে। রোজ সকালে নওলাখাদের বাড়িতে চা-বিস্কুট, সন্ধেবেলা তাস-আড্ডা-মদ্যপান, চোখের সামনে দেখতে দেখতে একটা সময় প্রায় অসুস্থই হয়ে পড়েন বিমলা। খেতওয়াতদের একমাত্র পুত্র অনিল চাকুরিজীবী, নিজেকে নিয়ে থাকতেন। মা-বাবার দাম্পত্য অশান্তির ব্যাপারে ছিলেন চূড়ান্ত উদাসীন।
‘নারীচরিত্র দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যা।’ মানসিক অশান্তিতে নিত্যদিন ক্ষতবিক্ষত হতে থাকা বিমলা ঠিক করলেন, পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দেবেন নওলাখা-দম্পতিকে। বীণার প্রতি আক্রোশ সহজবোধ্য। গিরিশের উপর তীব্র রাগ পরকীয়াকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি একা অশক্ত মহিলা, কাজটা করবে কে?
বিমলা ডেকে পাঠালেন খোকনকে। খেতওয়াতদের কোম্পানির দীর্ঘদিনের পিয়ন খোকন গিরি। একতলার অফিসে থাকে। প্রায় রোজই আসে ফ্ল্যাটে, খোকনের হাত দিয়ে খামভরতি টাকা বীণার কাছে মাঝেমাঝেই পাঠান যুগলকিশোর। বিমলা প্রস্তাব দিলেন, গিরিশ-বীণাকে খুনের বিনিময়ে এক লক্ষ টাকা দেবেন, চল্লিশ হাজার অগ্রিম। প্রথমে গররাজি ছিল খোকন, সে তো আর পেশাদার খুনি নয় যে ‘সুপারি’ নিয়ে মানুষ মারবে। বিমলা টাকার লোভ দেখাতেই থাকলেন, হাতে ধরিয়ে দিলেন নগদ চল্লিশ হাজার। মাথা ঘুরে গেল খোকনের। সে-সময়ে এক লাখ মানে অনেক টাকা। পিয়নের চাকরি ছেড়ে নিজের ছোটখাটো ব্যবসা চালু করার পক্ষে যথেষ্টেরও বেশি।
খোকন রাজি হয়ে গেল। একা মুশকিল হবে, শুরু করল সঙ্গীসাথি জোটানোর কাজ। কাঁচা টাকার লোভ বড় সাংঘাতিক, জুটেও গেল তিন শাগরেদ। রঞ্জিত রাও ওরফে রাজু, একসময় খেতওয়াতদের গাড়ি চালাত। চাকরি ছেড়ে দিয়ে কিছুদিন অন্য বেসরকারি সংস্থার গাড়ি চালিয়েছিল। তারপর আবার ফিরে এসে রামেশ্বর অ্যাপার্টমেন্টের-ই ৭ডি-র বাসিন্দা ওমপ্রকাশ ভুয়ানিয়ার ড্রাইভারের চাকরি নিয়েছিল। খোকন-রাজুর সঙ্গে যোগ দিল জগদীশ যাদব, মিস্টার খেতওয়াতের অফিসের সাফাইকর্মী। জগদীশই জোটাল কুকর্মের চতুর্থ শরিককে। কামিনীকুমার রায়, দক্ষিণ কলকাতার একটি গ্যারেজের কর্মী। চুক্তি হল, কাজ শেষ হলে প্রত্যেকে পাবে পঁচিশ হাজার করে। অগ্রিমের টাকা থেকে দশ হাজার করে ভাগ হল। দুটো দামি ইয়াশিকা ক্যামেরা কিনে ফেলল খোকন আর রাজু। কামিনী কিনল দামি সুটকেস।
খুনের ঘটনাপ্রবাহ ছিল এরকম। মনে রাখুন, ক্রিস্টমাস ইভের রাত। গমগম করছে বহুতল-প্রাঙ্গণ। গাড়ির স্রোত সন্ধে থেকেই, ঢুকছে-বেরচ্ছে। কেউ পার্টিতে যাচ্ছেন, কারও আবার বাড়িতেই উৎসবের আয়োজন। অতিথিদের অবিরাম আনাগোনা। কর্মীরাও উঠছেন-নামছেন সর্বক্ষণ। দিনটা ভেবেচিন্তেই বেছে ছিল খোকনরা। নওলাখাদের পুত্র-পুত্রবধূ যে ২৪ নয়, ২৬ তারিখে ফিরবেন, সে-খবর বিমলা আগাম জানিয়ে দিয়েছিলেন খোকনকে।
খোকন, রাজু এবং জগদীশ নিরাপত্তারক্ষীদের বহুদিনের পূর্বপরিচিত কর্মী। অপরিচিত বলতে কামিনী। যাকে সঙ্গে নিয়ে রাজু ন’টা নাগাদ উঠে গেল নিজের সাততলার কোয়ার্টারে, যা বরাদ্দ গৃহকর্মীদের জন্য। নিয়ম অনুযায়ী, রিসেপশনের রক্ষীরা আটকাল না। জগদীশ গেল একটু পরে, যোগ দিল রাজু আর কামিনীর সঙ্গে।
বিমলা খেতওয়াত ঠিক সাড়ে ন’টা নাগাদ বেল বাজালেন নওলাখাদের ফ্ল্যাটে। দরজা খুললেন বীণা নওলাখা। বিমলা বললেন, তাঁর স্বামী বোধহয় সকালে পানপরাগের কৌটোটা ফেলে গিয়েছেন, বাড়িতে খুঁজে পাচ্ছেন না,একটু যদি দেখা যায়। বীণা দেখেশুনে জানালেন, ‘না, এখানে তো নেই।’ ততক্ষণে বিমলার যা দেখার ছিল, দেখা হয়ে গিয়েছে। নিশ্চিত হয়ে গিয়েছেন, বাড়ির গৃহকর্মীরা কেউ নেই। প্রতিমা-মনিকা-শম্ভু কাজ শেষ করে বেরিয়ে গিয়েছে।
খোকন অপেক্ষা করছিল বিমলার নির্দেশমতো, নীচে ইন্টারকমের কাছে। ঠিক দশটায় বিমলার ফোন আসার কথা। যথাসময়ে ফোন এল। বিমলা জানালেন, লাইন ক্লিয়ার, এটাই মোক্ষম সময়। যুগলকিশোর ততক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছেন। পুত্র অনিল বেরিয়েছে পার্টিতে, রাত হবে ফিরতে।
খোকন সিঁড়ি দিয়ে সাততলায় উঠল, ডেকে নিল রাজু-জগদীশ-কামিনীকে। একটি বড় ব্যাগে সঙ্গে ছিল লোহার ব্লেড, শাবল ইত্যাদি। দশটা পাঁচে বেল বাজল নওলাখাদের ১০সি-র ফ্ল্যাটে। গিরিশ নওলাখা আইহোল দিয়ে দেখলেন খোকনকে, বহুদিনের পরিচিত মুখ। খুলে দিলেন দরজা, ঝাঁপিয়ে পড়ল খোকন আর দলবল। প্রতিরোধ ব্যর্থ হল গিরিশের। পাজামা-পাঞ্জাবি পরে ছিলেন, শাল ছিল গায়ে। ওই শালই গলায় পেঁচিয়ে খুন করল খোকন।
বেডরুমে ছিলেন বীণা, বেরিয়ে এসে চেষ্টা করলেন টেলিফোনের কাছে যাওয়ার। বৃথা চেষ্টা। ফোনের তার ততক্ষণে কেটে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। বীণাকে যথেষ্ট শারীরিক হেনস্থা করা হল, বেডরুমে পড়ে থাকা একটি শাড়ির প্রান্ত দিয়ে শ্বাসরোধের চেষ্টা হল, অন্য প্রান্ত সিলিংফ্যানে বেঁধে। চেষ্টা বিফল হওয়ায় বালিশ মুখে চেপে কেড়ে নেওয়া হল প্রাণবায়ু। এরপর গেস্ট রুমের আলমারি ভেঙে যথেচ্ছ লুঠপাট এবং সরে পড়া, দরজা বাইরে থেকে বন্ধ করে দিয়ে।
খোকন-রাজু-জগদীশ ফিরে গেল নিজেদের কোয়ার্টারে, স্নান করে শুয়ে পড়ল দিব্যি। কামিনীই একমাত্র বহিরাগত, ভোর হওয়ার আগে ব্যাগভরতি লুঠের সামগ্রী সমেত পালাল পাঁচিল টপকে, ঝিমোতে থাকা নিরাপত্তারক্ষীদের এড়িয়ে। ঠিক ছিল, লুঠের মাল পরে ভাগ হবে।
খোকনের জবানবন্দির ভিত্তিতে গ্রেফতার করা হল বিমলা খেতওয়াতকে। বিমলা অপরাধ স্বীকার করলেন। কয়েকদিনের মধ্যে পুলিশের জালে ধরা পড়ল রাজু আর কামিনী। জগদীশ পালিয়েছিল বিহারের প্রত্যন্ত জেলার বাড়িতে, ধরে আনলেন গোয়েন্দারা। লুঠ করা জিনিস খুনের পরের রাতেই ভাগ করে নিয়েছিল চারমূর্তি। উদ্ধার হল প্রচুর গয়নাগাটি, ঘড়ি, ঘর সাজানোর বহু দামি সামগ্রী। যা শনাক্ত করলেন প্রয়াত নওলাখা-দম্পতির পুত্র ও পুত্রবধূ।
১৯এ, শরৎ বোস রোডের বহুতল বাড়িটির প্রবেশপথ
আশ্চর্যের, ঘটনার পরের দু’দিনও খোকন-রাজু-জগদীশ ওই অ্যাপার্টমেন্টে কাজ করে গিয়েছে নির্বিকার। বিন্দুমাত্র স্নায়ুর চাপ ছাড়াই। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদের উত্তর দিয়েছে, চা এনে দিয়েছে তদন্তকারী দলের জন্য। একেই কি বলে ‘ক্রিমিনাল মাইন্ড’?
সুজিত মিত্র, লিখেছি আগেই, তদন্তকারী অফিসার ছিলেন। পদোন্নতির পর দীর্ঘদিন ওসি হোমিসাইড পদে চাকরি করেছেন সুনামের সঙ্গে। বছরদুয়েক আগে অবসর নিয়েছেন ডিসি স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চ হিসেবে। যত্নশীল এবং লড়াকু তদন্ত করেছিলেন।
যত্নের অংশবিশেষ প্রথমে বলে নিই। গড়ফা মেইন রোডের কমল স্টুডিয়ো থেকে খোকন ও রাজু কিনেছিল দুটি ইয়াশিকা ক্যামেরা। সেই স্টুডিয়ো থেকে বাজেয়াপ্ত করা হল সংশ্লিষ্ট ক্যাশমেমো দুটি। কামিনী অগ্রিম থেকে পাওয়া ভাগের টাকায় একটি বড় সুটকেস কিনেছিল ভবানীপুরের দোকান থেকে। সেই ক্যাশমেমোও বাজেয়াপ্ত হল। কামিনী গ্রেফতার হওয়ার পর দেখা গিয়েছিল, ডান পায়ের পাতায় ক্ষতচিহ্ন। পাঁচিল টপকে পালানোর সময় লোহার শলাকায় আঘাত লেগেছিল। পাঁচিলে দাগ ছিল রক্তের। সেই রক্ত যে কামিনীরই, প্রমাণ করতে হল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায়। ঘটনাস্থলের নানা জায়গা থেকে নেওয়া হাত-পায়ের ছাপ পাঠানো হল ফরেনসিক পরীক্ষায়, মিলে গেল চার আততায়ীর সঙ্গে। আদালতে গোপন জবানবন্দিতে দোষ কবুলও করল খোকন এবং রাজু।
পড়তে যতটা সহজ মনে হল, আদতে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংহত করার কাজটি তার চেয়ে ঢের বেশি কঠিন ছিল। গ্রেফতার-পরবর্তী তদন্ত আসলে মালা গাঁথার মতোই। ঠান্ডা মাথায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে একটি একটি করে প্রমাণ ঘটনা-পরম্পরা অনুযায়ী সাজিয়ে তবেই তৈরি হয় এধরনের জটিল মামলার চার্জশিট। মালাটি নিখুঁত গাঁথতে পারলে জাল কেটে বেরনোর রাস্তা থাকে না অভিযুক্তের, আইনের কাছে নতজানু হতে হয় নিরুপায়ভাবে।
তদন্তের প্রেক্ষিতে ‘লড়াকু’ শব্দটি লিখেছি আগের এক অনুচ্ছেদে, সচেতনভাবেই। তিন মাসের মধ্যেই পেশ হল চার্জশিট, শুরু হল বিচারপর্বের লড়াই। অন্যতম অভিযুক্ত রাজু নিজেই ইচ্ছে প্রকাশ করল রাজসাক্ষী হওয়ার। কাজ কিছুটা সহজ হল পুলিশের।
খেতওয়াত পরিবার অত্যন্ত বিত্তশালী ছিলেন। বিমলার জামিনের জন্য রাজ্যের এবং ভিনরাজ্যের প্রথিতযশা আইনজীবীদের লাগানো হয়েছিল। কলকাতা পুলিশের পক্ষে ছিলেন অভিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর শিশির ঘোষ। অন্যদিকে আইনি দুনিয়ার তারকাদের ছড়াছড়ি। বিচার চলাকালীন তীব্র চাপান-উতোরের সাক্ষী থাকল আদালত।
কিন্তু ওই যে লিখলাম, মালাটি গাঁথা হয়েছিল নিপুণ। ১৯৯৯ সালে আলিপুরের জেলা ও দায়রা আদালত বিমলা খেতওয়াত, খোকন গিরি, কামিনীকুমার রায় এবং জগদীশ যাদবকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করল। রাজসাক্ষী রাজু আগাগোড়া সহযোগিতা করেছিল। মুক্তি দেওয়া হয় ‘প্রসিকিউশন’-এর আবেদনের ভিত্তিতে।
মামলা গড়ায় হাইকোর্টে। যেখানে রাষ্ট্রের আর-এক প্রস্থ লড়াই এক ডজন নামজাদা আইনজীবীর সঙ্গে। হাইকোর্টও নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখল বিস্তর সওয়াল-জবাবের পর। সেটা ২০০৬ সাল।
পরের ধাপ সুপ্রিম কোর্ট। ততদিনে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বিমলা খেতওয়াত। দেহের একটি দিক প্রায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত, আরও নানা ব্যাধি বাসা বেঁধেছে শরীরে। স্বাস্থ্যজনিত কারণে বিমলাকে জামিন দেয় সর্বোচ্চ আদালত। একটু সুস্থ হলেই আত্মসমর্পণ করতে হবে ফের, এই শর্তে। বিমলা ফেরেন শরৎ বোস রোডের ফ্ল্যাটে।
সুপ্রিম কোর্টও শেষমেশ হাইকোর্টের রায়ের সঙ্গেই সহমত হয়। তার আগেই অবশ্য জাগতিক আদালতের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছিলেন বিমলা। ২০০৮-এর জুনের এক দুপুরে দশতলার বারান্দা থেকে ঝাঁপ দেন নীচে। মৃত্যু ঘটে মাটি ছোঁয়া মাত্রই। দেহের পাশে ওঁর ক্রাচটি পড়ে ছিল, যেটি সঙ্গে নিয়েই মরণঝাঁপ দিয়েছিলেন।
কেন আত্মহনন? ফের কারাবাসের আতঙ্ক? সামাজিক অসম্মানের গ্লানি, নাকি বিবেকদংশন? নাকি ‘জীবন যখন শুকায়ে যায়’, মুক্তি এভাবেই আসে ‘করুণাধারায়’?
১.০৭ মুখ ঢেকে যায় বিজ্ঞাপনে
[বিশ্বনাথ দত্ত হত্যামামলা
তদন্তকারী অফিসার অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়]
ভ্রু তুলিয়া একটু বিস্মিতভাবে ব্যোমকেশ বলিল –“বিজ্ঞাপন পড় না? তবে পড় কি?”
“খবরের কাগজে সবাই যা পড়ে, তাই পড়ি—খবর।”
“অর্থাৎ মাঞ্চুরিয়ায় কার আঙুল কেটে গিয়ে রক্তপাত হয়েছে আর ব্রেজিলে কার একসঙ্গে তিনটে ছেলে হয়েছে, এই পড়। ওসব পড়ে লাভ কী? সত্যিকারের খাঁটি খবর যদি পেতে চাও, তাহলে বিজ্ঞাপন পড়।”
আমি খোঁচা দিবার লোভ সামলাইতে পারিলাম না, বলিলাম— “ও, তাই না কি? কিন্তু খবরের কাগজওয়ালারা তাহলে ভারি শয়তান, সমস্ত কাগজখানা বিজ্ঞাপনে ভরে না দিয়ে কতক গুলো বাজে খবর ছাপিয়ে পাতা নষ্ট করে।”
ব্যোমকেশের দৃষ্টি প্রখর হইয়া উঠিল। সে বলিল— “তাদের দোষ নেই। তোমার মত লোকের চিত্তবিনোদন না করতে পারলে বেচারাদের কাগজ বিক্রি হয় না, তাই বাধ্য হয়ে ঐ সব খবর সৃষ্টি করতে হয়। আসল কাজের খবর থাকে কিন্তু বিজ্ঞাপনে। দেশের কোথায় কি হচ্ছে, কে কি ফিকির বার করে দিন-দুপুরে ডাকাতি করছে, কে চোরাই মাল পাচার করবার নতুন ফন্দি আঁটছে— এই সব দরকারী খবর যদি পেতে চাও তো বিজ্ঞাপন পড়তে হবে। রয়টারের টেলিগ্রামে ওসব পাওয়া যায় না।”
বড়তলা থানায় ফোনটা বেজেছিল কাকভোরে, পৌনে পাঁচটা নাগাদ।
—এখানে গণ্ডগোল হচ্ছে স্যার, প্রচুর লোক জমে গেছে। তাড়াতাড়ি আসুন।
—এখানে মানে?
—২সি, বিডন স্ট্রিট। খুন করে ফেলেছে স্যার।
—খুন?
ডিউটি অফিসার ফোন নামিয়ে রাখেন। সবে মিনিট পনেরো হল সকালের শিফটে বসেছেন। প্রথম ফোনটাতেই খুনের খবর? সাধে কি বলে, ‘মর্নিং শোজ় দ্য ডে!’ সকালই বুঝিয়ে দিচ্ছে, বাকি দিনটা কেমন যাবে?
বড়তলা থানা থেকে কতই বা দূরত্ব ঘটনাস্থলের? এক কিলোমিটার বড়জোর। পুলিশের জিপ যখন থামল ২সি বিডন স্ট্রিটের সামনে, অত ভোরেও অন্তত শ’তিনেক লোক। চিৎকার-চেঁচামেচিতে বোঝা দায়, ঠিক কী ঘটেছে। পুলিশের আবির্ভাবে সমবেত কোলাহল নিমেষে আরও উচ্চকিত, জানোয়ারটাকে আমরাই ফাঁসি দেব স্যার, আপনারা ফিরে যান!
২সি, বিডন স্ট্রিট
অপরাধের সুলুকসন্ধান পরে। পরিস্থিতি যা, এ তো আইনশৃঙ্খলার সমস্যা হতে যাচ্ছে। এমনিতেই জনবসতিপূর্ণ এলাকা, কৌতূহলী মানুষের ভিড় জমাট বাঁধছে দ্রুত। অফিসার ওয়ারলেস সেট হাতে নিলেন, বার্তা পাঠালেন থানায়। থানা থেকে যা অবিলম্বে পৌঁছল লালবাজার কন্ট্রোলে, “Commotion at Beadon Street over suspected murder. Reinforcement required as early as possible. Please inform superiors.”
থানা জানাল ওসিকে, লালবাজার জানাল ডিসি নর্থ আর ডিসি ডিডিকে। ওসি সাততাড়াতাড়ি ছুটলেন, হোমিসাইড শাখার অফিসাররাও। পার্শ্ববর্তী থানাগুলি থেকে বাড়তি ফোর্স রওনা দিল বিডন স্ট্রিটের উদ্দেশে। কন্ট্রোল রুম ঘটনাস্থলে অফিসারদের জানিয়ে দিল, “DC North and DC DD on way. Situation report every five minutes please.”
বিশ্বনাথ দত্ত হত্যা মামলা। বড়তলা থানা, কেস নম্বর ৬২/৯৪। তারিখ ৬/৩/৯৪, ভারতীয়
দণ্ডবিধির ১২০ বি/৩০২/২০১ ধারায়। অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, খুন এবং প্রমাণ লোপাট।
সূচনায় শরদিন্দুর ‘পথের কাঁটা’-র প্রারম্ভিক অংশের একটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করেছি।
উপায়ান্তর ছিল না। আলোচ্য মামলার ঘটনাপ্রবাহে নির্ণায়ক ভূমিকা ছিল সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের, যেখানে ব্যোমকেশের ভাষায়, “আসল কাজের খবর” ছিল।
৩১ জানুয়ারি, ১৯৯৪, সোমবার। চন্দননগরের বাড়িতে বসে আনন্দবাজার পত্রিকার সারিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের পাতায় চোখ বুলোচ্ছিলেন অভিজিৎ। চাকরির সন্ধানে আছেন, কর্মখালির বিজ্ঞাপন খুঁটিয়ে পড়েন। লিখে রাখেন, কোথায় কোথায় আবেদনপত্র পাঠাবেন। দেখতে দেখতেই নজর পড়ল জমি/বাড়ি বিক্রয়-এর কলামে। এটা কী?
‘নোটিস
কলিকাতা মিউনিসিপ্যালের অন্তর্ভুক্ত/ ২/সি, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, বড়তলা থানার অধীন বাড়ী বিক্রয় হইবে। উক্ত ঠিকানার বাড়ীর দুই অংশিদার ছাড়া, যদি কোন অংশিদার বা দাবিদার থাকেন, তাহা হইলে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ৭ দিনের মধ্যে এসে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। বিকাশ পাল এডভোকেট স্মল কজেজ কোর্ট। ২/১, কিরণ শংকর রায় রোড, কলিকাতা-১’
একবার নয়, দু’বার পড়লেন অভিজিৎ। কাগজ হাতে নিয়েই সোজা পাশের ঘরে, ‘বাবা! এটা দেখেছ?’
সকাল সোয়া ন’টা তখন। প্রাতরাশ সেরে অফিসযাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন অমরনাথ। ছেলেকে বিচলিত দেখে একটু অবাকই হলেন। অভিজিৎ আশৈশব শান্ত প্রকৃতির, অকারণ উত্তেজনার প্রকাশ তার স্বভাববিরুদ্ধ। কাগজটা টেনে নিলেন ছেলের হাত থেকে।
‘কী হল? কী বেরিয়েছেটা কী? দেখি…’
অমরনাথ দেখলেন, এবং অফিসে হাজিরার ব্যস্ততা সাময়িক অগ্রাধিকার হারাল। বসার ঘরের ল্যান্ডলাইন থেকে তৎক্ষণাৎ ফোন করলেন কলকাতার নম্বরে।
—সমর, আজকের আনন্দবাজার দেখেছিস? আটের পাতা, বিজ্ঞাপনের কলাম… জমিবাড়ি…
বিডন স্ট্রিটের তিনতলা বাড়িটি সাতের দশকের শেষাশেষি তৈরি করেছিলেন জগন্নাথ দত্ত। তিনি গত হলেন ’৯০-এর শুরুতে। স্ত্রী-ও প্রয়াত হলেন বছরতিনেকের মধ্যেই। উত্তরাধিকার সূত্রে বাড়ির মালিকানা পেলেন চার পুত্র, এক কন্যা।
বাড়ি বিক্রির নোটিস
বড় অমরনাথ ব্যাংকের আধিকারিক। সপরিবারে বাস চন্দননগরে। স্ত্রী সংসারধর্মে ব্রতী, পুত্র অভিজিৎ পড়াশোনার পাশাপাশি চাকরিপ্রত্যাশী। মেজো সমরনাথ পৈতৃক বাড়িতে থাকেন না, তবে কলকাতারই বাসিন্দা, চাকুরিজীবী। পরের ভাই বিশ্বনাথ, অকৃতদার। ইউনাইটেড ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার ধর্মতলা শাখার কর্মী। নির্বিরোধী মানুষ, নেশা বলতে দুটি, গান আর বিভিন্ন দেশের পুরনো মুদ্রা সংগ্রহ। রেকর্ড-ক্যাসেট কিনতেই ব্যয় হয়ে যায় বেতনের অর্ধাংশেরও বেশি। তিনতলায় দুটি ঘর নিয়ে অন্তর্মুখী জীবনযাপন।
পরের সন্তান অনুরাধা, বিবাহিতা। শ্বশুরবাড়ি কলকাতারই ফকির চক্রবর্তী লেনে।
সর্বকনিষ্ঠ অলোকনাথ কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল। স্ত্রী মমতা, এক শিশুপুত্র এবং দুই নাবালিকা কন্যাসহ থাকেন দোতলার দুটি ঘরে একটি আচ্ছাদিত বারান্দাসহ। অলোকনাথের ভায়রাভাই শিবশঙ্কর, ডাকনাম বাবু। কর্মহীন। ওই বারান্দাতেই তার নিশিযাপন।
একতলার ঘরগুলিতে ভাড়াটেরা থাকেন। মাসান্তে ভাড়ার সমবণ্টন হয় ভাইবোনদের মধ্যে। অমরনাথ-সমরনাথ-অনুরাধার ভাগের কয়েকটি ঘর খালিই পড়ে থাকে দু’তলা–তিনতলায়।
আনন্দবাজারের বিজ্ঞাপন নজরে আসার পর কালক্ষেপের প্রশ্ন ছিল না। অমরনাথ যোগাযোগ করলেন সমরনাথ ও অনুরাধার সঙ্গে। বিডন স্ট্রিটের বাড়ির মালিকানার অংশীদার তাঁরাও এবং তাঁদের অনুমতি ব্যতিরেকে বাড়ি বিক্রি আইনসিদ্ধ নয়, উকিলকে জানিয়ে দিলেন যৌথ চিঠিতে। ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহে।
প্রশ্ন ওঠা সংগত, বিশ্বনাথ এবং অলোকনাথকে কিছু জানালেন না কেন, কেন কিছু জানতে চাইলেন না? উত্তরে ভাইবোনদের সম্পর্কের সমীকরণ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত জরুরি।
বিশ্বনাথ, পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন, নিজের জগতে থাকতে ভালবাসতেন। নিস্তরঙ্গ দিনাতিপাত, সামাজিক মেলামেশায় তীব্র বীতস্পৃহা। বৈষয়িক আলোচনায় বরাবরের অনাগ্রহী। অলোকনাথের মানসিক অবস্থান অবশ্য আমূল বিপ্রতীপে। ভোগবিলাসে আকর্ষণ মজ্জাগত, অনায়াস বিচরণ রেসের মাঠে, দিনান্তে মেজাজি মদ্যপান, নিষিদ্ধপল্লিতে পরিচিত মুখ নিয়মিত যাতায়াতের সৌজন্যে।
বিশ্বনাথ ভাইয়ের জীবনযাত্রায় হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকতেন। কিন্তু সমরনাথ-অমরনাথ-অনুরাধার সঙ্গে অত্যন্ত তিক্ত সম্পর্ক ছিল অলোকনাথের। ছোটভাইয়ের উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের তীব্র বিরোধী ছিলেন ওঁরা। পারস্পরিক বাক্যালাপ বন্ধই ছিল একরকম, বাবা-মা গত হওয়ার পর বিডন স্ট্রিটের পৈতৃক বাড়িতেও আর পা-ই রাখেননি অন্যত্র বসবাসকারী ভাইবোনরা।
বিজ্ঞাপন দেখে ওঁরা ভাবলেন, আপনভোলা বিশ্বনাথকে ভুল বুঝিয়ে নিশ্চয়ই বাড়ি বিক্রির মতলব ফেঁদেছেন অলোকনাথ। উকিলকে তথ্যপ্রমাণসহ প্রতিবাদপত্র পাঠিয়ে আশ্বস্ত হলেন তিন ভাইবোন। যাক, বাড়ি বিক্রির সম্ভাব্য চক্রান্ত সমূলে বিনষ্ট করা গেল।
সমরনাথের কলকাতার বাইরে কাজ ছিল অফিসের, ফেরার কথা ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে। অমরনাথ ঠিক করলেন, সমরনাথ ফিরলে মার্চের প্রথম সপ্তাহে দু’জনে মিলে বিডন স্ট্রিটের বাড়িতে যাবেন। একটা হেস্তনেস্ত অলোকের সঙ্গে এবার না করলেই নয়। কী ভেবেছেটা কী? ‘ধাবু’কেও (বিশ্বনাথের ডাকনাম) বোঝানো দরকার। কাউকে কিছু না জানিয়ে রাজি হয়ে গেল অলোকের কথায়? টাকাপয়সার লোভ তো ধাবুর কোনওকালেই ছিল না, তা হলে?
‘তা হলে’-র উত্তর মিলল ৬ মার্চের ভোরে। আগের রাতেই অমরনাথ পুত্র অভিজিৎকে নিয়ে চন্দননগর থেকে পৌঁছলেন কলকাতায়। উঠলেন সমরনাথের বাড়িতে। ঠিক হল, তিনজনে রাত দুটো-আড়াইটে নাগাদ যাবেন বিডন স্ট্রিটে। অলোকের মর্নিং ডিউটি থাকলে ভোর পাঁচটায় বেরিয়ে যাবে। দেখাই হবে না সকালে গেলে। আর দেখা হলেও ডিউটির অজুহাতে আলোচনাটা হতে দেবে না। বেরিয়ে গিয়ে আর ফিরবেই না হয়তো দু’-তিনদিন। ধরতে হবে ঘুমনোর সময়।
ঘুমচোখে দরজা খুললেন অলোক, চমকে গেলেন দাদাদের ওই গভীর রাতে দেখে।
—তোমরা?
—অনেকদিন আসা হয়নি, খোঁজখবর নিতে এলাম। উপরে গিয়েছিলাম, ধাবুর ঘর দেখলাম ভিতর থেকে বন্ধ। ধাক্কা দিতে কেউ আওয়াজ দিল ভিতর থেকে, ‘বাদ মে আইয়েগা।’ ধাবু কই?
—ওহো, তোমাদের বলা হয়নি, ধাবুদা তো দিন পনেরো হল বারাসতে ঘরভাড়া নিয়ে চলে গেছে।
—মানে? হঠাৎ বারাসতে কেন?
—বলল, কিছুদিনের মধ্যেই ইউবিআই-এর বারাসত ব্রাঞ্চে বদলি হয়ে যাবে। এখান থেকে যাতায়াতের অসুবিধে হবে। তাই আগে থেকেই ওখানে একটা আস্তানা…
মাঝপথে থামিয়ে দেন অমরনাথ।
—তোর গল্পটা দাঁড়াচ্ছে না। কী হয়েছে বল? আর আমাদের ঘরগুলোও ভিতর থেকে বন্ধ কেন? খোলাই তো থাকে সবসময়। ধাবু কোথায়?
—বললাম তো বারাসত! বিশ্বাস না হয় দেখে এসো। ১১/১ ঝাউতলা লেন, বারাসত চৌরাস্তার কাছে। শুধুশুধু চোটপাট করছ কেন?
—করছি কি আর সাধে! আমাদের ঘর বন্ধ কেন? ধাবুর ঘরেই বা কারা? এসব কী করেছিস তুই? আমরা বারাসত থেকে ঘুরে এসে তোর সঙ্গে বোঝাপড়া করছি।
ততক্ষণে তর্কাতর্কি আর চেঁচামেচিতে বেরিয়ে এসেছেন একতলার ভাড়াটেরা। দু’তলা–তিনতলার ভিতর থেকে বন্ধ ঘরগুলি থেকেও বেরিয়ে এসেছেন এক অবাঙালি পরিবারের সদস্যরা। সমরনাথ পরিচয় জানতে চাইলে এক মাঝবয়সি ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, ‘মেরা নাম নন্দলাল সিং। অলোকবাবু আর বিশ্বনাথবাবু আপনা আপনা হিস্যা মুঝে বেচ দিয়া থোড়ে দিন পহেলে।’
—তার মানে? ওই ঘরগুলোর মালিক আমরা, কিনে নিয়েছেন মানে?
—আপ অলোকবাবুসে পুছিয়ে না! এগ্রিমেন্ট হ্যায় মেরে পাস। দেখ লিজিয়ে।
বাড়ি বিক্রির দলিল আনতে ঘরে ঢুকলেন নন্দলাল, আর সমরনাথ কলার চেপে ধরলেন ছোটভাইয়ের। অলোকনাথ তখন দৃশ্যতই কোণঠাসা, মুখে টুঁ শব্দটি নেই। মমতাও নিশ্চুপ, নতমস্তক। অমরনাথ নিরস্ত করলেন সমরনাথকে।
—আগে বারাসত যাই চল। ধাবুটার কী হল কে জানে! ফিরে এসে বাকি বোঝাপড়া করছি।
অমরনাথ–সমরনাথ-অভিজিৎ ট্যাক্সি করে রওনা দিলেন বারাসত, ফিরলেন রাত সোয়া চারটে নাগাদ। অলোক যে ঠিকানা বলেছিলেন, সেখানে অন্য পরিবার বাস করে। বিশ্বনাথের খোঁজ পাওয়া যায়নি। আশঙ্কাই সত্যি হয়েছে, ডাহা মিথ্যে বলেছেন অলোক।
ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল দুই দাদার। চড়থাপ্পড়ের অকৃপণ বৃষ্টিপাত হল অলোকের উপর, ‘বল কী করেছিস? পিটিয়েই মেরে ফেলব না হলে!’ চেপে ধরলেন একতলার ভাড়াটেরাও।
মিনিটপাঁচেকের বেশি ওই ঝড়ঝাপটা সহ্য করতে পারলেন না অলোক, স্বীকারোক্তি এল।
—ধাবুদাকে মেরে পুঁতে দিয়েছি।
—মানে?
‘মানে’ উদ্ধারে অবিলম্বে বড়তলা থানার নম্বর ডায়াল করলেন অভিজিৎ।
অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী পৌঁছনোর পর ভিড় ঠেলে ঢোকা গেল ২সি বিডন স্ট্রিটের অন্দরমহলে। হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছেন অলোকনাথ দু’তলার বারান্দায়, এক কোণে প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে মমতা। একতলার ভাড়াটেদের অনেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বারান্দার এদিক-সেদিক। অমরনাথ থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে। সমরনাথ বিধ্বস্ত, চোখের জল মুছছেন। অভিজিৎ সামলাচ্ছেন শোককাতর কাকাকে। ওসিকে দেখে অমরনাথ এগিয়ে এলেন।
—আসুন বড়বাবু, আমার নাম অমরনাথ দত্ত।
—কী হয়েছে? শুনলাম খুন…
কাঁদতে কাঁদতে সমরনাথ ছুটে যান অলোকনাথের দিকে। কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে থাকেন ছোটভাইয়ের।
—স্যার, এ খুন করেছে, এ! ধাবুকে খুন করে পুঁতে দিয়েছে। নিজের দাদাকে খুন করে জাল দলিল বানিয়ে বাড়ি বিক্রি করেছে, কুলাঙ্গার একটা, ফাঁসি দিন স্যার…কিছুতেই বলছে না কোথায় পুঁতে রেখেছে আমাদের ধাবুকে…
অফিসাররা বুঝলেন, এভাবে কাজের কাজ কিছু হবে না। একান্তে জিজ্ঞাসাবাদ দরকার। ক্রোধোন্মত্ত জনতার ভিড় ঠেলে অলোকনাথকে কোনওমতে নিয়ে যাওয়া হল বড়তলা থানায়।
‘ঘটনাটা পুরোটা বলুন। আপনি কলকাতা পুলিশের কর্মী। পুলিশের কায়দাকানুন জানেন। সত্যিটা তাড়াতাড়ি বললে ভাল। যত দেরি করবেন, তত বেশি ক্ষতি, এটা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না।’
অলোকনাথ বিস্তর মারধর খেয়েছেন দাদাদের হাতে একটু আগেই। ঠোঁট ফুলে গিয়েছে, চুল উস্কোখুস্কো, হাঁফাচ্ছেন। বলতে শুরু করলেন। রহস্য ক্রমে উন্মোচিত হল।
প্রায় পঁচিশ বছর আগে কতই-বা বেতন ছিল একজন কনস্টেবলের? স্ত্রী এবং তিন সন্তানের সংসার সামলে বেহিসাবি বিলাসব্যসন অসম্ভব। ইন্দ্রিয়ের তাড়নাকে সংযত রাখার ক্ষমতা অবশ্য কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল অলোকনাথের অনায়ত্ত ছিল। রেস-জুয়া-মদ-নারীসঙ্গের অভ্যাস ত্যাগ করার অক্ষমতা বাধ্য করেছিল ধারদেনায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়তে। পরিত্রাণের পথ খুঁজছিলেন মরিয়া অলোকনাথ।
পথের দিশা পেলেন একটাই, অনেক ভাবার পর। বাড়ির দু’তলা-তিনতলাটা যদি বেচে দেওয়া যায়, অর্থাগম হবে যথেষ্ট। কিন্তু বড়দা-মেজদা আর দিদি রাজি হবে? সম্ভাবনা শূন্য। ধাবুদা? বলে দেখা যেতে পারে একবার। বললেনও ’৯৩-এর নভেম্বরের শেষদিকে এবং হতাশ হয়ে পড়লেন বিশ্বনাথের প্রতিক্রিয়ায়।
—না না, বাড়ি বেচার প্রশ্ন আসছে কেন হঠাৎ? দিব্যি আছি তো।
বিশ্বনাথ ‘দিব্যি’ থাকতে পারেন, ধারদেনায় বিপর্যস্ত অলোকনাথ মোটেই স্বস্তিতে ছিলেন না। ভ্রাতৃহত্যার ষড়যন্ত্রের বীজ বপনে দেরি করলেন না বিশেষ। আশ্রিত ভায়রাভাই শিবশঙ্করকে শরিক করলেন পরিকল্পনার। চিত্রনাট্য রচনায় থাকল স্ত্রী মমতারও সক্রিয় অংশগ্রহণ। টাকার লোভে চক্রান্তে যুক্ত হলেন শিবশঙ্করের ভগ্নিপতি মৃণাল দত্ত। বাড়ি নিমতায়, পেশায় ব্যাংককর্মী। নিয়মিত যাতায়াত ছিল বিডন স্ট্রিটের বড়িতে।
জেরায় নাজেহাল অলোকনাথ মাঝেমাঝেই কেঁদে ফেলছেন, জবানবন্দিতে ছেদ টানছে স্বগতোক্তি, ‘এ আমি কী করলাম! ক্ষমা করে দিন স্যার!’
এসব কুম্ভীরাশ্রু অনেক দেখেছেন গোয়েন্দারা, বাকিটা বলতে বাধ্য করছেন নির্মোহ নৈপুণ্যে, তারপর কী হল?
—ব্রোকারদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। খদ্দেরও পেয়ে গেলাম কয়েকজন। মৃণাল আমার শালা, আমি আর মমতা মিলে বোঝালাম মৃণালকে, ধাবুদার নামে সই করতে হবে বেচাকেনার দলিলে, বিশ্বনাথ দত্ত সেজে। প্রথমে রাজি হচ্ছিল না, কিছু টাকা দিলাম। মৃণাল সামান্য চাকরি করত, রাজি হয়ে গেল।
—তারপর?
—নন্দলাল সিং নামে এক অবাঙালি খদ্দেরের সঙ্গে চুক্তি ফাইনাল হল। বাড়ি দেখতে এলেন নন্দলাল। ধাবুদা যখন অফিসে, তখন দেখালাম। মৃণালকে পরিচয় দিলাম বিশ্বনাথ দত্ত হিসেবে, আর মমতাকে নিজের দিদি অনুরাধা হিসেবে। দোতলা আর তিনতলার ঘরগুলো বেচার এগ্রিমেন্ট হল, সইসাবুদ জানুয়ারির মাঝামাঝি। মৃণাল-মমতা সই করল বিশ্বনাথ-অনুরাধা হিসেবে। অ্যাডভান্স হিসেবে ষাট হাজার মতো পেলাম।
নন্দলালদের তাড়া ছিল। তাগাদা দিচ্ছিলেন, কবে পজেশন পাবেন? দখল পাওয়ার এবং রেজিস্ট্রেশনের পর বাকি লাখদুয়েক দেওয়ার কথা হয়েছিল। ধাবুদা থাকলে কী করে পজেশন দেব? অ্যাডভান্স নিয়ে ফেলেছি, বাগুইআটির অশ্বিনীনগরে ফ্ল্যাট ভাড়াও হয়ে গেছে, যেখানে উঠে যাব ঠিক করেছিলাম বাড়ি বিক্রির পর।
—এর পর?
—ধাবুদাকে মেরে ফেলা ছাড়া তো আর উপায় ছিল না স্যার।
—তা কী উপায় করলেন?
—২২ জানুয়ারি রাতে ধাবুদা সাড়ে দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরল। বললাম বাড়িতে মিস্ত্রি লেগেছে, আমাদের বারান্দায় শুয়ে পড়ো। সরল মানুষ ছিল, বিশ্বাস করল। রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ আমি-শিবশঙ্কর-মৃণাল মিলে কম্বল চাপা দিয়ে মেরে ফেললাম। পরের দিন বিকেলেই পজেশন দিলাম নন্দলালকে। ওঁরা চলে এলেন, দখল নিলেন ঘরগুলোর। আমি বললাম, আমার ঘরটা কয়েকদিন পরেই ছেড়ে দেব। জিনিসপত্র শিফট করতে একটু সময় দরকার। নন্দলাল রাজি হয়ে গেলেন।
—বডি কোথায়?
—পুঁতে দিয়েছি স্যার।
—সে তো বুঝলাম, কিন্তু কোথায়?
অলোক নিরুত্তর। কলার ধরে ঝাঁকুনি দিতে কথা বেরল অস্ফুটে।
—নিমতলা ঘাটের কাছে স্যার।
—জায়গা দেখাতে পারবেন?
—হ্যাঁ স্যার।
কালবিলম্ব না করে গাড়ি ছুটল নিমতলা ঘাটে। অলোক একবার এ-জায়গা দেখাচ্ছেন, একবার ও-জায়গা। যেন দিকভ্রান্ত, অকস্মাৎ স্মৃতিভ্রষ্ট।
অপরাধীর এহেন অকাল স্মৃতিভ্রংশের সঙ্গে পরিচিত গোয়েন্দারা। বুঝলেন, সহজে কবুল করবেন না অলোকনাথ। একে লালবাজারে নিয়ে যাওয়া দরকার, থানায় হবে না। তবে তার আগে অলোকনাথের এবং বিশ্বনাথের ঘরটা সার্চ করা প্রয়োজন, সকালের তাড়াহুড়োয় আর হট্টগোলে করা যায়নি। স্থির হল, ঘরগুলো তল্লাশি করে seizure list তৈরি করে তারপর সোজা লালবাজার। অনেক সময় আছে, কতক্ষণ চেপে রাখবে সত্যিটা?
ফের বিডন স্ট্রিট। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা ততক্ষণে দখল নিয়ে ফেলেছেন বাড়ির।
বারান্দার এবং বাড়ির বাকি অংশের স্কেচম্যাপ তৈরির কাজ চলছে পুরোদমে। শিবশঙ্কর এবং মমতাকে আটক করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। দু’জনেরই মুখে কুলুপ। মৃণালের নিমতার বাসস্থানের খোঁজে টিম বেরিয়ে গিয়েছে। কাদের কাদের জেরা করা আশু প্রয়োজন, তৈরি হচ্ছে তালিকা। তদারকিতে ডিসি ডিডি স্বয়ং, সহায়তায় ডিসি নর্থ।
হোমিসাইড বিভাগের টিমে ছিলেন অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন আটাশ বছরের তরুণ সাব-ইনস্পেকটর, অধুনা ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার। অতনু ছিলেন অনুসন্ধিৎসু স্বভাবের, সজাগ মস্তিষ্ক এবং ক্ষুরধার বুদ্ধির সুবাদে প্রিয়পাত্র ঊর্ধ্বতন অফিসারদের।
তন্নতন্ন করে প্রতিটি ঘর খুঁজে যখন প্রস্তুতি চলছে seizure list-এর, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা খুঁজছেন বারান্দায় হাত বা পায়ের ছাপের নমুনা, অতনুও ঘুরে দেখছিলেন এঘর-ওঘর। হঠাৎই চোখ আটকে গেল নন্দলালের ঘরের দেওয়ালে। ঠাকুরের বেদি, যেমন আছে এবাড়ির অধিকাংশ ঘরে। কিন্তু এটার রং একটু অন্যরকম লাগছে না? একটু কাঁচা মনে হচ্ছে না চোখের দেখায়? বাকি দেওয়ালের রঙের সঙ্গে একটু তফাত যেন? ঘরের সমস্ত অংশ সাদা, এই বেদিটা একটু ক্রিমরঙা, সামান্য লালচেও না? বিদ্যুৎঝলক খেলে যায় অতনুর মাথায়।
—স্যার, একবার এদিকে আসবেন?
সিমেন্ট করা সেই বেদিটি, যার নীচে মৃতদেহ ছিল
তড়িঘড়ি এলেন ডিসি ডিডি সহ বাকিরা। আরে, সত্যিই তো! রং সামান্য আলাদা, আর কাঁচাও। অলোকনাথকে নিয়ে আসা হল বেদির সামনে। মিনিটদুয়েকের ধমকধামক এবং মৃদু চড়চাপড়ের পর ভেঙে পড়লেন দত্তবাড়ির কনিষ্ঠ পুত্র।
—ওখানেই ধাবুদাকে পুঁতে দিয়েছিলাম স্যার।
নিজেদেরই বাড়ির দেওয়ালে দাদাকে খুন করে পুঁতে দিয়ে বাড়ি বিক্রি, ‘পথের কাঁটা’-কে সরিয়ে দেওয়া? বাক্রুদ্ধ অভিজ্ঞ অফিসাররাও, সংবিৎ ফিরতে সময় লাগল কিছু। মিস্ত্রি ডাকা হল, বেদিতে কোদালের প্রথম কোপ পড়ার কিছু পরেই দুর্গন্ধ দখল নিল ঘরের। উদ্ধার হল দেহ, মৃত্যুর দেড় মাস পরে। ঘাড়ে-গলায়-বুকে সামান্য মাংস লেগে রয়েছে, শরীরের অবশিষ্ট প্রায় কঙ্কালে পর্যবসিত। জেরায় প্রকাশ্যে এল, কখন কীভাবে মৃত্যু এসেছিল তেতাল্লিশ বছরের বিশ্বনাথের, সহোদরের চক্রান্তে।
বিশ্বনাথ দত্ত-র কঙ্কাল
২২ জানুয়ারি, ১৯৯৪। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ বাড়ি ফিরলেন বিশ্বনাথ, ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে ব্যাংকের একটি বিচিত্রানুষ্ঠান দেখে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে যাবেন, মুখোমুখি অলোকনাথের সঙ্গে।
—ধাবুদা, আজ তুই আমাদের ঘরের লাগোয়া বারান্দাটায় শুয়ে পড়বি?
—কেন রে?
—না, ঘরগুলোর যা অবস্থা, মিস্ত্রি লাগিয়েছি একটু চুনকামের জন্য। তাড়াহুড়োয় বলা হয়নি আগে। আজ তিনতলাটা ধরেছে, কাল-পরশু দোতলাটা করবে।
বিশ্বনাথ দেখতেও পেলেন কয়েকটি সিমেন্টের বস্তা দু’তলা থেকে তিনতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে। ভাইকে বিশ্বাস করলেন। খাওয়াদাওয়া সেরে নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়লেন দু’তলায় ভাইয়ের ঘরের লাগোয়া বারান্দায়। মৃণাল পূর্বপরিকল্পনা মাফিক সাড়ে ন’টার মধ্যেই এসে পৌঁছলেন, অপেক্ষা করলেন অলোকনাথের ঘরে। যেখানে তখন উপস্থিত শিবশঙ্করও। এগারোটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল অলোকের পুত্র-কন্যারা। ঘড়ির কাঁটা যখন পেরল সাড়ে বারোটা, অলোক বেরলেন ঘর থেকে। ফিরলেন মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই।
—দাদা ঘুমিয়ে পড়েছে। মমতা, কম্বলটা দাও।
কম্বল নিয়ে শিবশঙ্কর, মৃণাল আর অলোক এলেন বারান্দায়, যেখানে বিশ্বনাথ গভীর
নিদ্রাচ্ছন্ন। শিবশঙ্কর দুই পা চেপে ধরলেন বিশ্বনাথের, মৃণাল হাত দুটো। অলোক কম্বল চাপা দিলেন দাদার মুখে, সর্বশক্তি প্রয়োগে চেপে ধরে থাকলেন প্রায় মিনিটসাতেক। হাত-পায়ের নিষ্ফল ছটফটানি ক্রমে থেমে এল বিশ্বনাথের। কম্বল মুখ থেকে তুলে নাকের কাছে হাত নিয়ে পরীক্ষা করলেন অলোকনাথ। চোখের পাতা টেনে দেখলেন…
নাহ্, নিশ্বাস পড়ছে না আর, কাজ হয়ে গেছে।
কাজ আরও বাকি ছিল, সম্পূর্ণ করলেন চক্রী-চতুষ্টয়, অলোক-মমতা-মৃণাল-শিবশঙ্কর। মিস্ত্রিদের দিয়ে কিছুদিন আগেই অলোক দু’তলার একটি ঘরে নতুন করে ভিত করিয়ে রেখেছিলেন ঠাকুরের বেদির। যেমন বেদি দেয়ালের সঙ্গে ছিল বিডন স্ট্রিটের বাড়ির অধিকাংশ ঘরেই। মজুত ছিল পর্যাপ্ত সিমেন্ট-বালিও।
বিশ্বনাথের নিস্পন্দ দেহকে বেদির মধ্যে পা মুড়িয়ে ঢোকানো এবং অতঃপর গাঁথনি, প্রমাণ লোপাটে ভোর হয়ে গেল প্রায়। মৃণাল ফিরে গেলেন নিমতার বাড়িতে, শিবশঙ্কর রোজকার মতো শুয়ে পড়লেন বারান্দায়, যেখানে ঘণ্টাখানেক আগেই ঘুমোচ্ছিলেন বিশ্বনাথ। এবং পাশের ঘরের দেওয়ালে দাদার মৃতদেহ গেঁথে দেওয়ার পর অলোকনাথ-মমতা ঘরে ফিরে নিদ্রা গেলেন নির্বিকার।
অলোক-মমতা-শিবশঙ্কর গ্রেফতার হয়েছিলেন মৃতদেহ আবিষ্কারের দিনই। মৃণাল ধরা পড়লেন পরের দিন, নিমতার বাড়ি থেকে।
তদন্তের দায়িত্ব ন্যস্ত হল অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরই। পুলিশকর্মী নিজের দাদাকে হত্যা করে পুঁতে রেখেছিলেন বাড়ির দেওয়ালে, অশ্রুতপূর্ব এই ঘটনায় শহর জুড়ে তুমুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিকই ছিল। যেমন স্বাভাবিক ছিল দ্রুত চার্জশিট পেশ করে শাস্তিবিধানের চাপ। অলোকনাথ যে প্রকৃতির মানুষ, পুলিশকে দেওয়া বয়ান সম্পূর্ণ অস্বীকার করবেন আদালতে, অনায়াসে অনুমেয়। পারিপার্শ্বিক প্রমাণের ভিত্তিতেই দোষী সাব্যস্ত করতে হবে অভিযুক্তদের, স্পষ্ট ছিল গোড়া থেকেই।
তদন্ত হল ম্যারাথন। অভিযুক্তদের গ্রেফতারির অর্থ, বিয়াল্লিশ কিলোমিটারের মধ্যে অতিক্রান্ত মাত্র দশ। বাকি বত্রিশে প্রমাণ সংগ্রহ, চার্জশিট পেশ এবং আদালতে বিচারান্তে শাস্তিপ্রাপ্তি। দৌড় শুরু করলেন অতনু। প্রমাণ একত্রিত করার জরুরি কাজটি সম্পন্ন করলেন নিখাদ নিষ্ঠায়, প্রত্যয়ী পরিশ্রমে।
বাগুইআটির অশ্বিনীনগরে অলোকনাথের ভাড়া করা ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার হল বিশ্বনাথের তিনটি ট্রাঙ্ক। যাতে ছিল পোশাকআশাক, প্রচুর পুরনো মুদ্রা আর গানের রেকর্ড-ক্যাসেট। অর্থলোভ কতটা অতলগামী করে ফেলে মানুষকে, তার প্রমাণ মিলল ২৪/এ, নিমতলা ঘাট স্ট্রিট-নিবাসী গোবিন্দ সর্দারের বাড়িতে। যাঁকে বিশ্বনাথের পাম্পসেট এবং কিছু আসবাবপত্র বেচে দিয়েছিলেন অলোকনাথ এবং কবুল করেছিলেন জেরায়।
বাড়ি বিক্রির দলিলে সই করেছিলেন অলোক-মৃণাল-মমতা। ত্রয়ীর হস্তাক্ষরের নমুনা (Specimen hand writing) সংগ্রহ করে পাঠানো হল ফরেনসিক পরীক্ষায়, প্রত্যাশিতভাবেই মিলে গেল হুবহু।
পুলিশ ট্রেনিং স্কুলের অস্ত্রাগারে (Armoury) কর্মরত ছিলেন অলোকনাথ। হাজিরা খাতা খুলে দেখা গেল, ২৩ জানুয়ারি ডিউটিতে এসে কিছু পরেই মেয়ের অসুস্থতার অজুহাতে বেরিয়ে যান। ফের কাজে যোগ দেন সপ্তাহখানেক পর। খুনটা হয়েছিল ২২-র রাতে। পরের সাতদিন অলোক ব্যস্ত থেকেছিলেন নন্দলালদের মালিকানা দেওয়ায় এবং অন্য সম্ভাব্য প্রমাণ লোপাটে। পারিপার্শ্বিক প্রমাণ হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কর্মক্ষেত্রে ওই ঘটনা-উত্তর অনুপস্থিতি।
সিমেন্ট-বালি অলোকনাথ কিনেছিলেন সৌমিত্র নায়ক নামের এক ইমারতি সামগ্রী বিক্রেতার থেকে, জানুয়ারির মাঝামাঝি। দোকান এবং দোকানের মালিক, দুই-ই চিহ্নিত হল। আদালতে রাখঢাকহীন বয়ান দিলেন সৌমিত্র, চিহ্নিত করলেন ক্রেতা অলোকনাথকে।
গ্রেফতারির পর থেকেই মৃণাল দত্ত তদন্তকারীদের বলে আসছিলেন, যে পাপ করেছি, তার ক্ষমা নেই। অভিনয় নয়, বাস্তবিকই অনুতাপদগ্ধ ছিলেন মৃণাল, মনে হয়েছিল অতনুর। মৃণাল সম্মত হয়েছিলেন আদালতে বিচারপতির কাছে জবানবন্দি (judicial confession) দিতে। ঘটনার বিবরণ দিয়েছিলেন পুঙ্খানুপুঙ্খ। যা চূড়ান্ত সহায়ক হয়েছিল শাস্তিবিধানে।
বয়ান নেওয়া হল আইনজীবী বিকাশ পালেরও, যিনি আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। বিকাশকে নিয়োগ করেছিলেন নন্দলাল, সম্পত্তি বেচাকেনায় কোনও আইনি জটিলতা রয়েছে কি না খতিয়ে দেখতে। বিক্রয়প্রক্রিয়া চলাকালীন অলোক আগাগোড়া বলে এসেছিলেন, তাঁরা দুই ভাই, এক বোন। বাড়ির দলিলপত্র পুরসভায় ‘সার্চ’ করে অন্য তথ্য পেয়েছিলেন বিকাশ। নথি বলেছিল, চার ভাই, এক বোন। প্রশ্ন করায় অস্বীকার করেছিলেন অলোক, এড়িয়ে গিয়েছিলেন উত্তর। অবধারিত সন্দেহের উদ্রেক হয়, কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন বিকাশ। যে বিজ্ঞাপন দেখা দিয়েছিল রহস্যভেদের প্রধান অনুঘটক রূপে। বিকাশও আদালতে চিহ্নিত করেছিলেন অলোক-মমতা-মৃণালকে।
মূল কাজটি অবশ্য তখনও অসমাপ্ত। প্রায় কঙ্কালে পরিণত দেহ যে বিশ্বনাথেরই, তার সন্দেহাতীত প্রমাণ।
ময়নাতদন্ত করেছিলেন অধ্যাপক ডা. অপূর্বকুমার নন্দী, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক অ্যান্ড স্টেট মেডিসিন বিভাগের তৎকালীন প্রধান। দীর্ঘ কর্মজীবনে কয়েক হাজার মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ডা. নন্দী রিপোর্টে লিখলেন, “Death in my opinion was caused by compression of neck, for example, throttling ante-mortem and homicidal in nature.” জানালেন, মৃতের বয়স আনুমানিক তেতাল্লিশ। বিশেষ তাৎপর্যের, অমরনাথ-সমরনাথ-অনুরাধা জানিয়েছিলেন, গজদাঁত ছিল বিশ্বনাথের। সেই গজদাঁতেরও উল্লেখ ছিল রিপোর্টে, যা চিহ্নিতকরণের পক্ষে অন্যতম পারিপার্শ্বিক প্রমাণ হিসেবে গ্রাহ্য হয়েছিল বিচারপর্বে।
দেহ শনাক্তকরণে তর্কাতীত প্রমাণ অবশ্য মিলেছিল ‘photographic superimposition’ পদ্ধতিতে। তদন্তকারী অফিসারের আর্জিতে যার সফল প্রয়োগ করেছিলেন কলকাতার Central Forensic Science Laboratory (CFSL)-র তৎকালীন ডেপুটি ডিরেক্টর ড. ভি কে কশ্যপ। ১৯৬০ সালে পঞ্চম শুক্লা হত্যা মামলায় কলকাতা তথা ভারতে প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল ‘সুপারইমপোজ়িশন’ পদ্ধতি। বিশ্বনাথ দত্তের খুনের মামলায় যার প্রয়োগ কলকাতা পুলিশের ইতিহাসে হয়েছিল দ্বিতীয়বার, চৌত্রিশ বছর পরে।
মৃতের করোটি। গজদাঁতের চিহ্নিতকরণের অন্যতম প্রমাণ
রিপোর্টে লেখা হয়েছিল, “The super-imposition test suggests that the skull and the mandible belonged to a person whose photographs were forwarded to me for test.”
ঘটনার ‘কী-কেন-কখন-কীভাবে’ এত নিখুঁত উঠে এসেছিল অতনুবাবুর চার্জশিটে, অভিযুক্তদের আইনজীবী হালে পানি পাননি। অলোকনাথ-মমতা–শিবশঙ্কর-মৃণালকে ফাঁসির সাজা শোনান সেশন কোর্ট, ২০০০ সালে। যা বহাল রাখেন কলকাতা হাইকোর্ট। সুপ্রিম কোর্ট অলোকের সাজা লঘু করে দণ্ডিত করেন যাবজ্জীবন কারাবাসে। বাকিদের, যাঁদের দীর্ঘ কারাবাস ততদিনে সম্পূর্ণ, মুক্তি দেওয়া হয়।
অলোকনাথ সম্প্রতি বহরমপুর জেলে পরলোকগত হয়েছেন। আপাতত ‘সর্বোচ্চ’ আদালতের বিচারাধীন হয়তো।
বিবরণীর সূচনা ‘পথের কাঁটা’-র উদ্ধৃতি দিয়ে। সমাপ্তিতেও নিই শরদিন্দুর শরণ। ব্যোমকেশের সেই বহুপঠিত কাহিনি মনে করুন, যাতে বৃদ্ধ করালীবাবুকে খুন করা হয়েছিল মেডালা আর ফার্স্ট সার্ভিকল ভার্টিব্রার সন্ধিস্থলে ছুঁচ ফুটিয়ে।
কল্পনার করালীবাবুর হত্যার সঙ্গে বাস্তবের বিশ্বনাথের খুনের বাহ্যত মিল নেই কোনও। তলিয়ে ভাবলে মনে হয়, সত্যিই নেই? মোটিভের মোহনায় তো মিলেমিশে গেছেই দুই হত্যাকাণ্ডের কল্পনা আর বাস্তব।
অর্থমনর্থম!
১.০৮ কী বিচিত্র এই দ্বেষ!
[হারুন হত্যামামলা
তদন্তকারী অফিসার আশিক আহমেদ এবং বিকাশ চট্টোপাধ্যায়]
—রোল নাম্বার ওয়ান?
—প্রেজেন্ট মিস!
—রোল নাম্বার টু?
—ইয়েস মিস!
—থ্রি?
—প্রেজেন্ট প্লিজ়!
—রোল নাম্বার ফোর?
উত্তর না পেয়ে অ্যাটেনডেন্সের খাতা থেকে মুখ তোলেন শাহনাজ, রিপন স্ট্রিটের Progressive Day School-এর ক্লাস ওয়ানের টিচার |
—হারুন কোথায়? আসেনি?
—না মিস, অ্যাবসেন্ট।
—ওকে, রোল নাম্বার ফাইভ?
রোল কল চলতে থাকে। সিক্স, সেভেন, এইট…
আমাদের হাওড়া-শিয়ালদায় যেমন অষ্টপ্রহর থিকথিক জনস্রোত, এখানেও তা-ই। একই ছবি মোটামুটি। কাঁধে বাক্সপ্যাঁটরা নিয়ে কুলিদের ব্যস্তসমস্ত যাতায়াত, এক প্ল্যাটফর্ম থেকে অন্যতে। ক্লান্তিহীন। হিন্দি-ইংরেজিতে ট্রেনের ঘোষণা মিনিটে মিনিটে, পাল্লা দিয়ে ইঞ্জিনের ধোঁয়ার কুণ্ডলী, আওয়াজের গজরানি। এক একটা ট্রেন থামছে, উগরে দিচ্ছে মানুষের দঙ্গল। এক একটা ছাড়ছে, টইটম্বুর যাত্রীদল সমেত। স্টেশনের বাইরে ট্যাক্সি-অটোর স্ট্যান্ডে নিত্যদিনের জটলা চালকদের। পান-বিড়ি-সিগারেটের আড্ডা। ওঁরা জানেন, খদ্দেরের অভাব এখানে হওয়ার নয়। সে কাকভোর হোক বা মাঝরাত। নির্জনতার প্রবেশ নিষেধ এ তল্লাটে।
বেরিলি জংশন। দিল্লি থেকে প্রায় আড়াইশো কিলোমিটার দূরের স্টেশন। উত্তরপ্রদেশের পাঁচটি ব্যস্ততম স্টেশনের তালিকা বানাতে বসলে বেরিলির অন্তর্ভুক্তি অবধারিত। এখান থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রোজ ছোটে দূরপাল্লার ট্রেন। সঙ্গে যোগ করুন যাত্রীবোঝাই লোকাল ট্রেনের দৈনন্দিন কু-ঝিকঝিক আর যথেষ্ট সংখ্যায় পণ্যবাহী গাড়ির প্রাত্যহিক আসা-যাওয়া।
বেরিলি জিআরপি (Government Railway Police) থানাকেও শশব্যস্ত থাকতে হয় চব্বিশ ঘণ্টাই। দিনে গড়ে দশটা মিসিং ডায়রি হবেই। বাচ্চাদের অনেকেই দলছুট হয়ে যায় রোজ, কপাল নেহাত খারাপ না হলে পাওয়া যায় খোঁজাখুঁজির পর। আর বড় স্টেশন মানেই, কে না জানে, পকেটমারদের যৌবনের উপবন, বার্ধক্যের বারাণসী। বেরিলিও ব্যতিক্রম নয়। সকাল-সন্ধে মিলিয়ে পকেটমারির অভিযোগ জমা পড়ে ডজন ডজন। রাত বাড়লে সাইডিং-এর আধো-অন্ধকারে মদ-জুয়ার মোচ্ছব তো রোজকার উপদ্রব। প্ল্যাটফর্মের এমাথা-ওমাথা টহলদারি চালাতেই হয় তিন শিফটে। মর্নিং, ইভনিং, নাইট। ঢিলেমির জো নেই এতটুকু।
সন্ধে তখন রাতের চৌকাঠে পা দেব-দেব করছে। প্ল্যাটফর্মে টহল দিতে দিতেই বড় স্টিলের ট্রাঙ্কটা নজরে এল দুই কনস্টেবলের।
এখানে এভাবে পড়ে কেন? কুলি নিয়ে এসে রেখেছিল? ট্রেনে ওঠাতে ভুলে গেছে, আর যার জিনিস সে-ও খেয়াল করেনি? না কি কেউ রেখে গিয়ে কিছু কিনে-টিনে আনতে গেছে, চলে আসবে শিগগির? কিন্তু এভাবে কোনও পাহারা ছাড়া মালপত্র ফেলে রেখে গেলে হাওয়া হয়ে যেতে আর কতক্ষণ? থানায় নিয়ে যাওয়াই ভাল, না হলে একটু পরেই হয়তো কেউ এসে কান্নাকাটি জুড়বে, আমার ট্রাঙ্ক চুরি হয়ে গেছে, অমুক প্ল্যাটফর্মের তমুক জায়গায় রাখা ছিল। মালপত্র আকছার চুরি হয় এই স্টেশনে, নতুন কিছু নয়।
ধরাধরি করে ট্রাঙ্ক আনা হল থানায়। ওসি এবং অন্য অফিসাররা উলটেপালটে দেখলেন। নাহ, কোথাও এমন কিছু লেখা নেই, যা থেকে মালিকের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। ওসি সিদ্ধান্ত নিলেন, খুলেই দেখা যাক কী আছে ভিতরে, জিনিসপত্র থেকে যদি সন্ধান মেলে মালিকের।
তালা ভাঙা হল এবং ট্রাঙ্কের ভিতরের দৃশ্যে আঁতকে উঠলেন বেরিলি জিআরপি থানার কর্মী-অফিসাররা। যাঁরা লাশ দেখে অভ্যস্ত এবং হঠাৎ মৃতদেহ দেখে যাঁদের বিচলিত হওয়ার কারণ নেই কোনও।
হারুন রশিদ হত্যা মামলা। পার্ক স্ট্রিট থানা, কেস নম্বর ৫৩৯। তারিখ ১৫/৮/৯৪। ধারা ৩৬৪/৩০২/২০১/৩৪ আইপিসি। খুনের উদ্দেশ্যে অপহরণ, খুন, প্রমাণ লোপাট এবং একই অপরাধের উদ্দেশ্যে একাধিকের সম্মিলিত পরিকল্পনা। মহম্মদ হাদিস সপরিবারে থাকতেন পার্ক স্ট্রিট থানা এলাকার ২২/২এ, ব্রাইট স্ট্রিটে। আদি বাড়ি বিহারের গয়া জেলায়। চাকরির সন্ধানে আটের দশকের মাঝামাঝি চলে আসেন কলকাতায়। চেষ্টাচরিত্রের পর চাকরি জোটে অজন্তা লেদার্স ফ্যাশন লিমিটেডে। ইলিয়ট রোডের কাছে সিরাজুল ইসলাম লেনে কোম্পানির ফ্যাক্টরি, তৈরি হয় চামড়ার জিনিসপত্র। কাজে ফাঁকি দেওয়া হাদিসের ধাতে ছিল না। দক্ষ কর্মী হিসেবে অল্পদিনেই মালিকের অত্যন্ত বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছিলেন।
ছোট পরিবার, সুখী পরিবার। স্ত্রী, নয় বছরের ছেলে হারুন আর বছর চারেকের ফুটফুটে মেয়ে। যার সেভাবে নামই ঠিক হয়নি এখনও। বাবা-মা-দাদা যে যেমন খুশি ডাকে আদর করে।
ছেলেমেয়েকে কলকাতায় পড়াবেন, ইচ্ছে ছিল হাদিসের। হারুন একটু বড় হতেই গয়ার স্কুল থেকে ছাড়িয়ে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। একটু বেশি বয়সেই হারুনকে ভরতি করলেন রিপন স্ট্রিটের ‘Progressive Day School’-এ ক্লাস ওয়ানে। হারুন তখন নয়। সালটা ১৯৯৪।
স্কুল শুরু হত সকাল সাড়ে সাতটায়। ছুটি বারোটায়। ট্রামে করে হারুনকে স্কুলে পৌঁছে দিতেন হাদিস। ছুটির পর কখনও হেঁটে, কখনও ট্রামে, একাই সাধারণত বাড়ি ফিরত হারুন। খেয়েদেয়ে কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিয়েই বিকেলে পাড়ায় ফুটবল পেটাতে ছুটত।
১৩ অগস্টের বিকেলে অন্যরকম হল। ফুটবল নিয়ে দাপানো তো দূরের কথা, স্কুল থেকে বাড়িই ফিরল না হারুন। সাড়ে বারোটার মধ্যে যে ছেলে চলে আসে, তিনটে পেরিয়ে সাড়ে তিনটে বেজে গেলেও তার পাত্তা নেই। কোথায় গেল? কী হল হারুনের?
খবর গেল হাদিসের কাছে, সব কাজ ফেলে বাড়ি ফিরলেন তড়িঘড়ি।
হারুনের স্কুল
খোঁজ-খোঁজ। স্কুলে ছোটা হল প্রথমে। দারোয়ান জানালেন, ছাত্ররা সবাই রোজকার মতো বেরিয়ে গিয়েছে। আলাদা করে হারুনকে খেয়াল করেননি। বন্ধুদের বাড়ি যেতে পারে? খোঁজখবর হল। নেই। পাড়াপ্রতিবেশীরা ভিড় জমালেন, এলেন অফিসের সহকর্মীরাও। হাদিস খবর দিলেন চার ঘনিষ্ঠ শুভানুধ্যায়ীকে। ছুটে এলেন মহম্মদ সামসুদ্দিন, কুদ্দুস আলম, মহম্মদ একলাখ এবং দীর্ঘদিনের প্রতিবেশী আলমগির।
চারজনই বহুদিনের পরিচিত হাদিসের। সবারই বয়স তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে। একলাখ ছাড়া গয়ারই বাসিন্দা সবাই, কর্মসূত্রে কলকাতায়। সামসুদ্দিন অনেকদিনের বন্ধু, ছোটখাটো কাপড়ের ব্যবসা আছে। বন্ধুর সঙ্গে যৌথভাবে ৩৬, আগা মেহেন্দি লেনে একটা ছোট দু’কামরার ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিলেন হাদিস বছরখানেক হল। গ্রামের বাড়ি থেকে আত্মীয়পরিজনরা প্রায়ই আসে, থাকতে দেওয়ার তো একটা জায়গা চাই। সেই উদ্দেশ্যেই বাড়ি ভাড়া।
মহম্মদ একলাখের বাড়ি বিহারের ছাপড়ায়। কাজ করতেন অজন্তা লেদার্সেই, হাদিসের সুপারিশেই চাকরি। কৃতজ্ঞ ছিলেন স্বাভাবিক কারণেই, হাদিসের পরিবারের যে-কোনও বিপদে-আপদে ঝাঁপিয়ে পড়তেন সবার আগে। দীর্ঘ অসুস্থতার কারণে ফ্যাক্টরির চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন সম্প্রতি, টুকটাক ব্যবসাপাতিতে দিন গুজরান। অবিবাহিত, বাবার সঙ্গে থাকেন ৪, দেদার বক্স লেনের একটা দু’কামরার ভাড়াবাড়িতে।
আলমগির একটা গাড়ির যন্ত্রাংশ মেরামতির দোকান চালান ইলিয়ট রোডের কাছে। থাকেন সপরিবারে ব্রাইট স্ট্রিটে, হাদিসের বাড়িতে নিয়মিত আসা-যাওয়া। দুই প্রতিবেশীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সম্পর্ক। সুখ-দুঃখে একে অন্যের পাশে থাকেন নিঃস্বার্থ।
হারুনের হারিয়ে যাওয়ার খবরে সবচেয়ে বিচলিত কুদ্দুস আলম। যিনি ভীষণ প্রিয় ছিলেন বালক হারুনের। ‘কুদ্দুস চাচা’ বলতে অজ্ঞান। ফুটবলের নেশা চাচাই ধরিয়েছিলেন। আগা মেহেন্দি রোডে সামসুদ্দিন-হাদিসের ভাড়ার ফ্ল্যাটে থাকতেন। হাদিস অস্থায়ী পার্টটাইম কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলেন কুদ্দুসকেও, ওই অজন্তা লেদার্স ফ্যাক্টরিতেই।
সারারাত ছোটাছুটি করেও যখন খোঁজ মিলল না হারুনের, পরের দিন সকালে, ১৪ অগস্ট, পার্ক স্ট্রিট থানায় মিসিং ডায়রি করলেন হাদিস। GDE (জেনারেল ডায়রি এন্ট্রি) নম্বর ১৫১৫। পুলিশকে জানালেন না, আগের দিন, ১৩ অগস্ট, বিকেল সোয়া তিনটে নাগাদ ফ্যাক্টরিতে একটা ফোন এসেছিল।
—হাদিসভাই, আপনার ফোন…
অজন্তা লেদার্সের বহুদিনের কর্মী ফজলুল ডাক দেন কাজে ব্যস্ত হাদিসকে।
—আমার? কে?
বলল না। আপনাকে খুঁজছে।
হাদিস রিসিভার কানে দেন। ওপার থেকে ভাঙাভাঙা গলায়, থেমে থেমে বলতে থাকে অপরিচিত।
—আপনার ছেলে আমাদের কাছে। আজ রাত দশটা নাগাদ পার্ক সার্কাসের ৪ নম্বর ব্রিজের মুখে দাঁড়াবেন। পঁচিশ হাজার টাকা একটা কালো ব্যাগে নিয়ে আসবেন। আমাদের লোক থাকবে। মাথায় লাল টুপি, ডানহাতে ঘড়ি। ওকে ব্যাগটা দিয়ে দেবেন। পুলিশে জানাতে পারেন। তবে জানালে আর ছেলেকে জীবিত পাবেন না। টাকা পেলে কাল সন্ধের মধ্যে ছেলেকেও পাবেন। আর একটা কথা, একা আসবেন। চালাকি পছন্দ করি না আমরা।
ফোন কেটে যাওয়ার পর হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল হাদিসের। পঁচিশ হাজার? মাসমাইনের চাকরি, চলে যায় মোটামুটি। এখন বিকেল সোয়া তিনটে। রাত দশটার মধ্যে এত টাকা জোগাড় হবে কী করে? ফোনে একবার হারুনের সঙ্গে কথা বলতে চাওয়ার কথাও মাথায় এল না। একবার ‘আব্বা’ ডাকটা শুনতে পেলে মনটা শান্ত হত একটু।
সামসুদ্দিন হাজার দুয়েক দিলেন, কুদ্দুস-একলাখ দিলেন হাজার খানেক করে। আলমগির জোগাড় করলেন চার হাজার। ফ্যাক্টরির মালিক খুবই পছন্দ করতেন হাদিসকে, বিপদে পাশে দাঁড়ালেন। দিলেন পাঁচ হাজার। পাড়া-প্রতিবেশীদের কাছে ধার আর নিজের সঞ্চয় থেকে কুড়িয়ে-বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে গেল পঁচিশে। ব্রাইট স্ট্রিটের বাড়ি থেকে পার্ক সার্কাস আর কতটুকু? রাত সাড়ে ন’টা নাগাদ হেঁটেই রওনা দিলেন কালো ব্যাগ হাতে। একাই।
সোয়া দশটা বাজল, ক্রমে সাড়ে দশটা, অপেক্ষা করতে করতে একসময় ঘড়ির কাঁটা দশকে অগ্রাহ্য করে এগারো ছুঁল। কোথায় সেই মাথায় লাল টুপি, ডানহাতে ঘড়ি? সাড়ে এগারোটা অবধি ধৈর্য ধরেও যখন কেউ এল না, একরাশ উদ্বেগ-আশঙ্কা-দুশ্চিন্তা নিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটা দিলেন হাদিস।
মাথা কাজ করছে না আর। কোথায় গেল ছেলেটা? কারা কিডন্যাপ করল? কেন? বাড়িতে ইতিমধ্যেই অবস্থা সঙ্গিন। স্ত্রী নাওয়া-খাওয়া প্রায় বন্ধই করে দিয়েছেন। মেয়ে বারবার জানতে চাইছে দাদার কথা। কী করবেন এখন?
আত্মীয়স্বজন-পাড়াপ্রতিবেশী সবাই গতকাল থেকে একই কাটা রেকর্ড বাজিয়ে চলেছে, সব ঠিক হয়ে যাবে। ভাল লাগছে না আর শুনতে। কী ঠিক হয়ে যাবে? হারুনকে ফিরে না পেলে কীভাবে ঠিক হয়ে যাবে সব? যার যায়, তারই যায়। অন্যরা কী করে বুঝবে হারুনের মুখটা মনে পড়লেই ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কোথায় আছে, কেমন আছে ছেলেটা?
পুলিশে জানানো দরকার এবার। মুক্তিপণ চেয়ে ফোনের কথাটা বলব? না কি আপাতত মিসিং ডায়েরি করে রেখে অপেক্ষা করা উচিত পরের ফোনের? কিডন্যাপাররা হয়তো আজ ইচ্ছে করেই টাকাটা নিল না, দূর থেকে নজর রাখছিল? না, আর একদিন দেখি, পুলিশকে বললে যদি জানতে পেরে যায় ওরা, মেরে ফেলে হারুনকে? আর ভাবতে পারেন না হাদিস।
মুক্তিপণের ফোনের ব্যাপার চেপে যাওয়া হল ১৪ তারিখ সকালের মিসিং ডায়েরিতে। কিন্তু সারাদিন অপেক্ষার পরও যখন আর ফোন এল না টাকা চেয়ে, বিপর্যস্ত হাদিসকে নিয়ে সামসুদ্দিন-কুদ্দুস-একলাখ-আলমগির এবং কয়েকজন সহকর্মী পার্ক স্ট্রিট থানায় এলেন সেদিনই সন্ধেবেলায়। সব খুলে বললেন হাদিস, অভিযোগ দায়ের হল। তদন্তের দায়িত্ব নিলেন সাব-ইনস্পেকটর আশিক আহমেদ, যিনি বর্তমানে তপসিয়া থানার ওসি।
থানা থেকে যখন বেরচ্ছেন লেখাজোকা শেষ হওয়ার পর, হাদিস দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি, পরের
দিনই ফিরে আসতে হবে আবার, চরম দুঃসংবাদ পেয়ে।
যা যা সঙ্গে থাকে ওই বয়সের স্কুলছাত্রের সঙ্গে, সব ছিল। খাতাবই স্কুলব্যাগের ভিতর, ওয়াটারবটল, টিফিনবক্স। স্কুলের ইউনিফর্ম পরা বালকের নিথর দেহ পড়ে ট্রাঙ্কের ভিতর।
শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে, গলায় আঙুলের স্পষ্ট দাগ দেখে অনুমান করতে অসুবিধে হয় না বেরিলি থানার ওসি-র। পরিচয়ও জানা যায় সহজেই, প্রত্যেকটি খাতায় নাম লেখা আছে গোটা গোটা অক্ষরে।
—স্যার লড়কা কা নাম হারুন রশিদ, কলকাত্তা কা কোই Progressive Day School কা স্টুডেন্ট লাগতা হ্যায়।
—স্কুল কা ফোন নম্বর পতা করো য্যায়সে ভি হো … অউর কলকাত্তা ট্রাঙ্ককল বুক করো জলদি ….
১৫ অগস্টের রাত সাড়ে ন’টা তখন।
রাত পৌনে এগারোটায় যখন বেরিলি থেকে ফোন এল হারুনের স্কুলে, ধরার লোক বলতে শুধু একজন দারোয়ান। যিনি ঘুমচোখে ফোন তুললেন এবং খবর শুনে সঙ্গে সঙ্গে জানালেন প্রিন্সিপালকে। যিনি এক মুহূর্ত দেরি না করে খবর দিলেন হাদিসকে। বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজন নিয়ে হাদিস ছুটলেন থানায়।
পার্ক স্ট্রিট থানার তৎকালীন ওসি ব্যোমকেশ ব্যানার্জি ট্রাঙ্ককলে কথা বললেন বেরিলি
জিআরপি-র ওসি-র সঙ্গে। সিদ্ধান্ত হল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাদিসকে নিয়ে পার্ক স্ট্রিট থানার একটি দল রওনা দেবে বেরিলিতে। অজন্তা লেদার্স ফ্যাক্টরির মালিক খবর পেয়ে মাঝরাতেই চলে এসেছিলেন থানায়। বললেন, হাদিসের প্লেনভাড়া তিনি দেবেন, সকালের ফ্লাইটে দিল্লি পৌঁছে সেখান থেকে গাড়িতে বেরিলি বিকেলের মধ্যে পৌঁছে যাওয়া যাবে।
সাততাড়াতাড়ি টিকিট জোগাড়ে সাহায্য করল থানা, প্লেনেই যাওয়া হল ১৬ অগস্টের ভোরে। হাদিসের সঙ্গে সামসুদ্দিন ছাড়াও গেলেন আলমগির। হাদিসের স্ত্রী ততক্ষণে শয্যা নিয়েছেন, অসংলগ্ন কথা বলতে শুরু করেছেন। সামলানোর জন্য কলকাতায় থেকে গেলেন কুদ্দুস-একলাখ।
বেরিলি পৌঁছতে ১৬ অগস্ট বিকেল হয়ে গেল। ছেলের দেহ শনাক্ত করলেন হাদিস, এবং করেই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। পোস্টমর্টেম বেরিলিতেই হল। যেমন ভাবা গিয়েছিল, শ্বাসরোধ করেই মারা হয়েছিল হারুনকে। শরীরের অন্য কোথাও কোনও ক্ষতচিহ্ন ছিল না।
দিনেদুপুরে একটা বাচ্চা ছেলেকে কিডন্যাপ করল কে বা কারা, এবং দেহ পাওয়া গেল কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরের বেরিলি স্টেশনে, ট্রাঙ্কবন্দি অবস্থায়! এমনটা কখনও ঘটেনি কলকাতা পুলিশের ইতিহাসে। কারা ঘটাল?
১৫ অগস্টের মাঝরাতেই ঘণ্টাখানেক আলাদা করে হাদিসের সঙ্গে কথা বলেছিলেন অফিসাররা। পরের দিন সকালে ফ্লাইট, পুত্রশোকে বাক্রুদ্ধ। তবু কিছু প্রশ্ন তো না করলেই নয়।
—কোনও শত্রু ছিল আপনার?
—না স্যার, ছাপোষা মানুষ, বউ-বাচ্চা নিয়ে থাকি। কোনও শত্রুতা নেই।
—কাউকে সন্দেহ হয়?
—না স্যার। হারুনকে কেন মারল স্যার? ও তো কোনও ক্ষতি করেনি কারওর। আমার সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। কাউকে সন্দেহ হয় না। কাকে সন্দেহ করব? আচ্ছা বডি কি সত্যিই হারুনের? কোথাও কোনও ভুল হচ্ছে না তো?
একমাত্র ছেলের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছে ট্রাঙ্কে, সুদূর উত্তরপ্রদেশে। মাথা কাজ না করারই কথা। এই মানসিক অবস্থায় কিছু জানতে চাওয়া এবং ঠিকঠাক উত্তরের প্রত্যাশা করাটাই অনুচিত। হাদিসকে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আসেন তদন্তকারী অফিসার আশিক। থানায় ফেরার পথে মাথায় পাক খেতে থাকে একাধিক সম্ভাবনা।
প্রথম প্রশ্ন, কিডন্যাপ যে বা যারা করেছে, সে বা তারা মুক্তিপণের টাকা নিতে এল না কেন পার্ক সার্কাসে চার নম্বর ব্রিজের কাছে? টাকা না পেয়েই মেরে দিল? এমন তো হওয়ার কথা নয়।
প্রশ্ন নম্বর দুই, পঁচিশ হাজার টাকার জন্য অপহরণ এবং খুন? পেশাদার গ্যাং খোঁজখবর নিয়ে কাজে নামে। যার থেকে মুক্তিপণ চাইব, তার সেটা দেওয়ার মতো সামর্থ্য আছে কি না সেটা নিশ্চিত জেনে নেয় আগেভাগে খোঁজখবর করে। হাদিস সামান্য চাকুরে, মাস গেলে সাকুল্যে মাইনে হাজার তিনেক। তিনি কোত্থেকে পঁচিশ হাজার দেবেন এক কথায়? ন্যূনতম হোমওয়ার্ক করল না অপহরণকারীরা?
তিন, মোটিভটা কী? টাকা যে নয়, বোঝাই যাচ্ছে। হাদিস অল্পক্ষণের জেরায় বলেছেন, কোনও শত্রু নেই। তা হলে? বেরিলি থেকে ফিরুন, তারপর হাদিসকে আর একবার বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ না করলেই নয়। পারিবারিক কোনও ঝামেলা, যার উৎস আদৌ কলকাতাতেই নয়, গয়ার বাড়িতে? বা অন্য কোথাও? ফ্যাক্টরিতে কোনও গোলমাল?
চার, মৃতদেহ বেরিলি স্টেশনে পৌঁছল কী করে? এত জায়গা থাকতে বেরিলি কেন? দেহ লোপাটের অনেক জায়গা আছে শহরে বা তার কাছেপিঠে। হারুন স্কুল থেকে ১৩ তারিখ বেরিয়েছিল ছুটির পর। আর বাড়ি ফেরেনি। বডি পাওয়া গিয়েছে ১৫ তারিখ রাতের দিকে বেরিলি স্টেশনে। অপহরণের পর হারুনকে নিয়ে ট্রেনে করে বেরিলি রওনা দিয়েছিল কিডন্যাপাররা? খুনটা ট্রেনে হয়েছিল?
পাঁচ, দিনের বেলা, রিপন স্ট্রিটের মতো জনবসতিপূর্ণ এলাকায় একটা ছেলেকে কে বা কারা তুলে নিয়ে গেল, কেউ দেখল না? অস্বাভাবিক নয়? তা হলে কি পরিচিত কেউ যুক্ত? কাল প্রথম কাজ, স্কুলে যাওয়া। হারুনের ক্লাসে এবং অন্য ছাত্রদের কাছে জানতে চাওয়া, কেউ কিছু দেখেছিল? দারোয়ান এবং অন্যান্য কর্মীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন।
ছয়, পুরনো ক্রাইম রেকর্ড আজই ঘাঁটতে হবে, প্রয়োজনে রাত জেগে। শহরে গত পাঁচ বছরে কতগুলো কিডন্যাপিং হয়েছে, কেসগুলোর সমাধান হয়েছে কি না, হলে অভিযুক্তরা এখন কোথায়, জেলে না জামিনে বাইরে, খোঁজ নিতে হবে। পুরনো কিডন্যাপারদের ছবি জোগাড় করতে হবে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের CRS (Crime Record Section) থেকে।
সাত, নতুন কোন গ্যাং? কিডন্যাপিং ছিঁচকে অপরাধীর কম্মো নয়। সাধারণত পেশাদার এবং পোড়খাওয়া গ্যাং-ই করে থাকে। পঁচিশ হাজারের জন্য একটা বাচ্চাকে তুলে নিয়ে গিয়ে মেরে দেওয়া, নাহ, হিসেব মিলছে না। একেবারে আনকোরা কোনও চক্র হলে অবশ্য অন্য কথা। পঁচিশ হাজার খুব বেশি টাকা নয় হয়তো, কিন্তু নেহাত কমও না, বিশেষ করে যদি কোনও বেপরোয়া উঠতি গ্যাং হয়।
আট, ঘুরেফিরে আটকে যাওয়া সেই প্রথম প্রশ্নেই, যে বা যারাই কাজটা করুক, টাকা তো হাতে আসেইনি। তার আগেই মেরে দিল? টাকা হাতে পাওয়ার পর মেরে ফেলার ঘটনা আছে। অপহৃতের পক্ষে যাতে পরে কিডন্যাপারদের চিনিয়ে দেওয়ার সুযোগ না থাকে, অনেক গ্যাং টাকা পাওয়ার পর খুন করে সেই সম্ভাবনাটুকুও নির্মূল করে দেয়। কিন্তু এক্ষেত্রে তো সেই থিয়োরিও খাটছে না। তা হলে?
নয়, বাবা-মাকে বাদ দিলে হারুনের সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিল কুদ্দুস। হারুনের সঙ্গে রোজই ফুটবল মাঠে অনেকটা সময় কাটাত কুদ্দুস, গল্পগুজব করত। হারুনের ব্যাপারে কুদ্দুসের সঙ্গে কালই কথা বলা দরকার। কে সবচেয়ে কাছের বন্ধু ছিল, কী খেতে ভালবাসত, অন্য পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদি, জানা জরুরি।
যেমন দরকার সামসুদ্দিন, আলমগির আর একলাখকেও জিজ্ঞাসাবাদের। ওঁরা ঘনিষ্ঠ ছিলেন হাদিসের। পরিবারের সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যেতে পারে। এবং শোক সামলে কিছুটা ধাতস্থ হলে হাদিসের স্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলা দরকার। বাইরে থেকে আর কতটুকুই বা বোঝা যায়, কে বলতে পারে খুনের মোটিভ হয়তো আদৌ মুক্তিপণ নয়, অজানা অভাবিত কিছু?
১৬ অগস্ট, ১৯৯৪, সোমবার সকাল পৌনে আটটা। সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনে আড়মোড়া ভাঙছে শহর।
ফার্স্ট পিরিয়ড চলছে Progressive Day School-এ। আশিক পৌঁছলেন জনাদুয়েক অফিসারকে নিয়ে, ডেকে নিয়েছেন কুদ্দুসকেও। প্রিন্সিপালের সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা সেরে নিলেন আশিক। ঘটনার কথা এখনও কাগজে বেরোয়নি, তবে আজকের মধ্যে জানাজানি হবেই। কাল ফলাও করে বেরবেই ন’বছরের স্কুলছাত্রের অপহরণ এবং খুনের খবর। তার আগে ছাত্রদের কিছু না জানাতে অনুরোধ করলেন স্কুল কর্তৃপক্ষকে। স্কুলের শিক্ষক-অশিক্ষক সমস্ত কর্মীদের তালিকা প্রয়োজন। আর, ক্লাস ওয়ানের ছাত্রদের সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার, কখন সম্ভব?
—এখনই চলুন, তবে বাচ্চারা যাতে ভয় পেয়ে না যায়, সেটা একটু …
—শিয়োর।
ক্লাসে ঢুকেই আশিক বুঝতে পারেন, বোকার মতো কাজ করে ফেলেছেন। ইউনিফর্ম পরে আসা ঠিক হয়নি, সিভিল ড্রেসে আসা উচিত ছিল। ক্লাস ওয়ান, কতই বা বয়স ওদের? বইখাতা নিয়ে কচিকাঁচার দল, বসে আছে বেঞ্চে। পুলিশ দেখে ভয় পেয়ে গেছে, চোখেমুখে শঙ্কার জ্যামিতি।
—এই পুলিশ আঙ্কল তোমাদের সঙ্গে কিছু কথা বলবেন। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।
ক্লাসটিচার শাহনাজের আশ্বাসে যে বিশেষ কাজ হয়নি, বাচ্চাদের দেখেই বোঝেন আশিক। লাভ হবে না জেনেও মুখ খোলেন, এসেই যখন পড়েছেন।
—হারুন, তোমাদের বন্ধু, আজকেও অ্যাবসেন্ট। ও বোধহয় দুষ্টুমি করে বাড়িতে না বলে অন্য কোথাও একটা লুকিয়ে রয়েছে। ওর বাবা-মা খুব চিন্তা করছেন। লাস্ট ফ্রাইডে যখন ছুটি হয়েছিল, তোমরা কি কেউ ওর সঙ্গে বেরিয়েছিলে?
পিনড্রপ সাইলেন্স।
—কেউ বলতে পারবে মনে করে, স্কুল থেকে বেরনোর পর হারুন কোনদিকে গিয়েছিল? তোমরা কেউ ছিলে সঙ্গে?
বাচ্চারা স্পিকটি নট।
আশিক বেরিয়ে আসেন। নাহ, এভাবে হবে না। কাল-পরশু অন্য অফিসারকে সিভিল ড্রেসে পাঠিয়ে টিফিন টাইমে কয়েকজন বাচ্চার সঙ্গে আলাপ জমাতে হবে। ব্রাইট স্ট্রিটের আশেপাশে, মানে হারুনের বাড়ির কাছাকাছি, স্কুলের অন্য কোন কোন ছাত্রের বাড়ি, সেটা বার করতে হবে স্কুলের রেজিস্টার থেকে। ওদের সঙ্গে কথা বলা দরকার।
প্রিন্সিপালের ঘরে ফিরে আসা হল। রয়েছেন আরও দু’-তিনজন সিনিয়র টিচার। ছাত্রদের
নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে ভাবনাচিন্তা করার প্রয়োজন, অভিভাবকদের ছাড়া ছুটির পর বাচ্চাদের বেরতে দেওয়া না-দেওয়া নিয়ে নতুন নিয়ম চালু করার সময় হয়েছে, এইসব আলোচনা চলছে টুকটাক। কথাবার্তায় ছেদ পড়ে শাহনাজের আওয়াজে।
—স্যার, একটা কথা ছিল।
প্রিন্সিপাল তাকান। শাহনাজের পাশেই একটু ভীতসন্ত্রস্ত মুখে দাঁড়িয়ে এক ছাত্রও।
—স্যার, সাব্বির, হারুনের ক্লাসমেট। কিছু বলতে চায় মিস্টার আশিককে। তখন ভয় পেয়ে গিয়েছিল হঠাৎ পুলিশ দেখে।
আশিক ঝটিতি উঠে দাঁড়ান। বাচ্চাটা কিছু দেখেছিল? কী বলতে চায়? ক্লু বলতে এখনও পর্যন্ত কিছুই হাতে নেই। বাচ্চাটার থেকে মিলতে পারে আদৌ?
—আঙ্কল, ফ্রাইডে ছুটির পর আমি আর হারুন একসঙ্গে বেরিয়েছিলাম। রোজই একসঙ্গে যাই।
—ফ্রাইডেতে কী হল?
—বাড়ির কাছে এসে হারুনকে ‘বাই’ বলার সময় একটা লোক হারুনকে ডাকল।
—তোমার বাড়ি কোথায়?
—কাছেই।
—তারপর?
—তারপর হারুন খুশি মনে লোকটার সঙ্গে চলে গেল।
—খুশি মনে?
—খুশি মনে।
—লোকটাকে দেখলে চিনতে পারবে?
—ইয়েস স্যার।
—স্যার নয়, আঙ্কল।
আশিক গাল টিপে দেন সাব্বিরের। দ্রুত চিন্তা করতে থাকেন। বলছে, দেখলে চিনতে পারবে। মানে চেহারাটা মনে আছে। ছবি আঁকানো দরকার। একটা আলোর রেখা দরকার ছিল, সেটা বাচ্চাটা দিয়েছে। ক্যাডবেরি চকোলেট তো প্রাপ্যই একটা।
বাচ্চাটির হাত ধরে বেরিয়ে আসেন শাহনাজ। পিছুপিছু আশিক, প্রিন্সিপাল এবং অন্যান্য শিক্ষকরা। আশিক হাঁক দেন, কুদ্দুস, একটা ক্যাডবেরি কিনে আনো তো চটপট।
কুদ্দুস দাঁড়িয়ে ছিলেন গেটের কাছে, পুলিশের গাড়ির পাশেই। আশিকের ডাকে পিছন ফেরেন এবং ফুট বিশেক দূরে দাঁড়িয়ে থাকা কুদ্দুসকে দেখে শাহনাজের হাত জোরে চেপে ধরে সাব্বির।
—কী হল?
—মিস, ওই আঙ্কলটা! ওর সঙ্গেই হারুন খুশি মনে চলে গেছিল ফ্রাইডে।
আশিক মুহূর্তে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। কুদ্দুসও। দু’জনে চোখাচোখি হয়। কয়েক সেকেন্ড মাত্র, কুদ্দুস রাস্তার দিকে দৌড় শুরু করার উপক্রম করতেই চিৎকার শুনতে পান গাড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা সহকর্মী অফিসার।
—ধরো ওকে!
থানার গাড়ির ড্রাইভারও ব্যাপার বুঝে লাফিয়ে নামেন। পালাবার পথ ছিল না কুদ্দুসের। কত দৌড়বে? উসেইন বোল্ট তো নন।
শেষমেশ কুদ্দুস? হারুনের কুদ্দুসচাচা? কিন্তু কেন?
—একা করিনি স্যার! একলাখও ছিল।
পার্ক স্ট্রিট থানার ওসি-র চেম্বারে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে থাকা কুদ্দুসের মুখ থেকে অস্ফুটে বেরোয় কথাগুলো। সঙ্গে সঙ্গে থানার গাড়ি স্টার্ট দেয় দেদার বক্স লেনে, একলাখের ঠিকানায়।
—কেন করলি ওইটুকু বাচ্চাকে খুন?
কুদ্দুসের জবানবন্দিতে খুলতে থাকে রহস্যের জট। এবং মোটিভের বৃত্তান্ত শুনে তাজ্জব হয়ে যান অফিসাররা। এত তুচ্ছ কারণে ন’বছরের একটা ছেলেকে এভাবে মেরে ফেলা যায়?
—হাদিসভাইয়ের জন্যই একলাখ আর আমি চাকরিটা পেয়েছিলাম। সামসুদ্দিনভাই, আমার আর একলাখ, দু’জনেরই দূরসম্পর্কের আত্মীয় হন। হাদিস খুব মানত সামসুদ্দিনভাইয়ের কথা। উনি অনুরোধ করায় ফেলতে পারেননি। মালিককে অনেক বলেকয়ে আমাদের চাকরিটা পাইয়ে দিয়েছিল হাদিসভাই।
—বেশ, তা সেই হাদিসের ছেলেকেই খুন করে কি ঋণশোধ করলি?
ফের দু’হাতে মুখ ঢাকে কুদ্দুস।
—মাথায় শয়তান ভর করেছিল স্যার। আমি চাইনি এর মধ্যে জড়াতে, একলাখের কথাতে করে ফেলেছি…
—ওটা তুই আগে ধরা পড়েছিস বলে বলছিস। একলাখ আগে ধরা পড়লে বলত, তোর কথাতে করেছে। দেখা আছে ওসব। মারলি কেন বাচ্চাটাকে?
—চাকরি পাওয়ার পর হাতে কিছু পয়সা আসত স্যার মাস গেলে। আগে তো এর থেকে ওর থেকে চেয়েচিন্তে চালাতে হত। আমি আর একলাখ প্রায় রোজই মদ খেতাম চাকরি জোটার পর। কাজে যেতে দেরি হয়ে যেত প্রায়ই। একদিন সুপারভাইজার খুব বকাবকি করল, কাজে ফাঁকি দেওয়ার জন্য নোটিস ধরাল। আমরা দু’জন সামসুদ্দিনভাইকে বললাম হাদিসভাইকে বলতে। হাদিসভাই মালিককে বোঝাল, আর একবার শেষ সুযোগ দিতে। মালিক অন্ধের মতো ভালবাসতেন হাদিসভাইকে। সুযোগ দিলেন, চাকরিটা বেঁচে গেল।
—তারপর?
—কিছুদিন আমরা মন দিয়ে কাজ করলাম, তারপর আবার যেই কে সেই। একলাখ শরীরের উপর এত অত্যাচার করত যে অসুস্থই হয়ে পড়ল। ফিরে গেল ছাপড়ার বাড়িতে। প্রায় ছ’মাস পরে ফিরল এই মাসখানেক আগে। ফ্যাক্টরিতে গেল, মালিক বলল, আর কাজে নেবে না। একলাখ কাজের মধ্যেই মদ খেত, হাদিসভাই অনেক বারণ করা সত্ত্বেও শুনত না। মালিক কিছুতেই আর কাজে নিল না।
একলাখ আবার ধরল সামসুদ্দিনভাইকে। এবার আর হাদিসভাই রাজি হল না মালিককে অনুরোধ করতে। স্পষ্ট বলে দিল, অনেকবার সাবধান করেছি, শুধরোসনি। আমার কথায় মালিক শেষ সুযোগ দিয়েছিল, সেই কথার দাম দিসনি, আমি এখন কোন মুখে বলব? তুই অন্য চাকরি খুঁজে নে। তর্কাতর্কি হল খুব।
—একলাখের ব্যাপারটা বুঝলাম। কিন্তু তুই তো দিব্যি চাকরি করছিলি…
—কোথায় আর করছিলাম স্যার? চাকরি তো টেম্পোরারি, পার্টটাইম। মালিক কিছুতেই পার্মানেন্ট করছিল না। সুপারভাইজার রিপোর্ট দিয়েছিল, দেরি করে আসি, কাজে ফাঁকি দিই। একলাখকে যখন আর কাজে রাখল না কোম্পানি, আমিও চিন্তায় পড়ে গেলাম। দরবার করলাম হাদিসভাইয়ের কাছে, তুমি একবার বললেই চাকরিটা পাকা হয়ে যায়। মাইনেটা বাড়ে। এত অল্প টাকায় আর চলছে না।
হাদিসভাই মুখের উপর বলে দিল, এখন বছরখানেক মুখ বুজে কাজ কর। দেখলি তো
একলাখের অবস্থা। সবাই জানে তোর আর একলাখের ব্যাপারস্যাপার। এখন কোনও চান্সই নেই পার্মানেন্ট হওয়ার, বেশি হইচই করলে যেটা আছে, সেটাও যাবে।
ভীষণ রাগ হয়ে গেল আমার। সেদিনই চাকরি ছেড়ে দিলাম। হাদিসভাইকে বললাম, তোমার দয়ার চাকরি আমি পায়ের তলায় রাখি। হাদিসভাইও রেগে গেল। বলল, তোদের দু’জনকে চাকরি জোগাড় করে দেওয়াই ভুল হয়েছে আমার।
—হুঁ…
—অমন ঝামেলা তো কতই হয়। আমি অত মনে রাখিনি স্যার। মিটমাট হয়ে গিয়েছিল। হাদিসভাইদের বাড়ি তারপরও যেতাম, হারুনকে ফুটবল খেলতে নিয়ে যেতাম। একলাখ কিন্তু চাকরি যাওয়াটা ভুলতে পারছিল না। একদিন ওর দেদার বক্স লেনের বাড়িতে ডাকল। মদ কিনে এনেছিল, অনেক রাত অবধি খেলাম। একলাখ আমার মনে বিষ ঢোকাল।
—আর তুই সে-বিষ ঢুকতে দিলি?
—মাথার ঠিক ছিল না স্যার। হাতে কাজকম্মো কিছু নেই। একলাখ বোঝাল, আমাদের দু’জনের চাকরি ইচ্ছে করলেই হাদিসভাই বাঁচাতে পারত। কিন্তু করেনি। শোধ নেব ওর জীবনটাও তছনছ করে দিয়ে। আমার যে কী ভূত চেপেছিল মাথায়, রাজি হয়ে গেলাম।
ছক কষলাম দু’জনে মিলে। হারুনকে কিডন্যাপ করব, পঁচিশ হাজার চাইব। টাকা নিয়ে দেশে ফিরে গিয়ে ব্যবসা করব। হারুনকে মেরে ফেলতেই হবে, ছেড়ে দিলে তো বলেই দেবে আমাদের নাম।
—কিন্তু টাকা তো আনতেই গেলি না … কেন?
—কী করে যাব স্যার? যেদিন দুপুরে হারুনকে তুললাম, সেদিন সন্ধে থেকে তো হাদিসভাইয়ের সঙ্গে। এখানে খুঁজছি, ওখানে খুঁজছি হারুনকে, কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে। হাদিসভাই টাকা নিয়ে বেরল সাড়ে ন’টায়, আমাদের বলল, তোরা থাক, ভাবিজানকে সামলা। মেয়েটাকে দ্যাখ।
তখন আমার বা একলাখের ব্রাইট স্ট্রিট থেকে বেরনোর উপায়ই ছিল না। ঘরভরতি লোক, কান্নাকাটি চলছে। প্ল্যান ভেস্তে গেল আমাদের।
—হারুনকে মারলি কখন?
কীভাবে খুন হয়েছিল হারুন, ফিরে দেখা ফ্ল্যাশব্যাকে।
১৩ আগস্ট, ১৯৯৪। স্কুল ছুটি হল, সাব্বিরের সঙ্গে বেরল হারুন, হেঁটে বাড়ি ফিরবে রোজকার মতো। আবদুল লতিফ স্ট্রিটে সাব্বিরের বাড়ির কাছে একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল কুদ্দুস। আর একটু দূরে একলাখ। কুদ্দুস হাত নেড়ে ডাকল হারুনকে। কুদ্দুসচাচাকে হঠাৎ ওখানে দেখে খুব খুশি হারুন, বায়না ধরল আইসক্রিমের। কুদ্দুস বলল, বেশ আমার বাড়িতে চলো। ওখানে আইসক্রিম আনব, খাওয়ার পর ব্রাইট স্ট্রিটে পৌঁছে দেব। একলাখও যোগ দিল কুদ্দুস-হারুনের সঙ্গে। একলাখের সঙ্গে তেমন ঘনিষ্ঠ ছিল না হারুন। তবে চিনত বাবা আর কুদ্দুসচাচার বন্ধু হিসেবে।
হারুনকে নিয়ে কুদ্দুস-একলাখ গেল ৩৬ আগা মেহেন্দি লেনের ভাড়াবাড়িতে। পরিকল্পনা ছিল ওখানেই খুনটা করার। ঢোকার মুখে দেখা হয়ে গেল এক প্রতিবেশীর সঙ্গে, যিনি হারুনের গাল টিপে আদর করে দিলেন। হারুনকে নিয়ে বাড়িতে ঢোকার সাক্ষী রাখা ঠিক হবে না, এই ভেবে হারুনকে নিয়ে যাওয়া হল একলাখের দেদার বক্স লেনের আস্তানায়। এই বলে, আইসক্রিম একলাখ চাচার বাড়িতে আছে।
যাওয়ার পথে দেখা হল শেখ সাহাবুদ্দিনের সঙ্গে। দেদার বক্স লেনেই যাঁর সবজির দোকান। হারুনের বাবাকে চেনেন, সেই সূত্রে হারুনকেও। আদর করে বললেন, টফি খাবে? হারুন বলল, না না, আইসক্রিম খেয়ে বাড়ি ফিরব।
কোথায় আইসক্রিম? দেদার বক্স লেনের ফ্ল্যাটে ঢোকার পরই হারুন শুনল, কুদ্দুসচাচা বলছে একলাখচাচাকে, আর দেরি করে লাভ নেই, শেষ করে দিই!
কুদ্দুস-একলাখ গলা টিপে ধরলেন হারুনের। দম বন্ধ হয়ে মৃত্যু আসতে আর কতক্ষণ? কী-ই বা প্রতিরোধ সম্ভব ওইটুকু বাচ্চার পক্ষে?
বড় স্টিলের ট্রাঙ্ক কিনে কুদ্দুস দিনকয়েক আগে রেখে দিয়েছিল আগা মেহেন্দি লেনের বাড়িতে। রিকশা নিয়ে কুদ্দুস ফের গেল আগা মেহেন্দি লেনের ফ্ল্যাটে। ট্রাঙ্ক নিয়ে ফিরল দেদার বক্স লেনে। হারুনের দেহ ট্রাঙ্কে ঢুকিয়ে তালাবন্ধ করে দেওয়া হল।
যেমন আগে থেকেই ভাবা ছিল, ট্রাঙ্কবন্দি দেহ নিয়ে বেরল দু’জনে। এবং বেরিয়ে কাছেই
পেমেন্টাল গার্ডেন লেনের একটা পিসিও বুথ থেকে মুক্তিপণ চেয়ে একলাখ ফোন করল হাদিসকে। এরপর ট্যাক্সি নিয়ে সোজা হাওড়া স্টেশন।
বিকেল ৪-১৭ মিনিটের হাওড়া-কাঠগোদাম এক্সপ্রেসের লেডিজ় কম্পার্টমেন্টে কুদ্দুস-একলাখ তুলে দিল ট্রাঙ্ক। যা প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে পৌঁছল বেরিলিতে। ট্রেন জংশনে থামার পর যাত্রীরা নেমে গেলে সাফাইকর্মীদের চোখে পড়েছিল। কেউ হয়তো ফেলে গেছেন, এই ভেবে প্ল্যাটফর্মে ট্রাঙ্ক নামিয়ে রেখেছিলেন। সান্ধ্য টহলদারিতে চোখে পড়েছিল বেরিলির জিআরপি-র কর্মীদের।
রহস্য উন্মোচনের পর বাকি তদন্তভার পড়েছিল ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের হোমিসাইড শাখার তৎকালীন সাব-ইনস্পেকটর বিকাশ চট্টোপাধ্যায়ের উপর। যিনি সফল কর্মজীবন শেষে অবসর নিয়েছিলেন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার হিসেবে।
কুদ্দুসকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে, খবর পেয়ে গিয়েছিল একলাখ। পালিয়েছিল রাজ্য ছেড়ে। সহজে পাকড়াও করা যায়নি, বিহারে গোয়েন্দারা দিনের পর দিন ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকা সত্ত্বেও। অক্টোবরের শেষে দিনদুয়েকের জন্য এসেছিল কলকাতায়, সোর্স মারফত খবর পেয়েছিলেন বিকাশ। বিহারে আর ফেরা হয়নি একলাখের, ঠাঁই হয়েছিল শ্রীঘরে।
বিকাশ ছিলেন সেই গোত্রের অফিসার, যাঁরা কোনও ফাঁকফোকর রাখতেন না তদন্তে, ছেঁটে ফেলতেন ন্যূনতম ‘চান্স ফ্যাক্টর’ও। সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রস্তুত করেছিলেন পেশাদারি পারদর্শিতায়। জাল বুনেছিলেন নিপুণ, যাতে হীনতম অপরাধের শাস্তি পায় অভিযুক্তরা।
ট্রাঙ্কটা কিনেছিলেন কুদ্দুস মল্লিকবাজারের একটা দোকান থেকে, ২২০ টাকা দিয়ে। দোকান চিহ্নিত হল কুদ্দুসের বয়ান অনুযায়ী, বাজেয়াপ্ত করা হল সংশ্লিষ্ট ক্যাশমেমোর কপি। দোকানদার কুদ্দুসকে চিনিয়ে দিলেন আদালতে। হ্যাঁ, এই লোকটাই কিনেছিল।
মুক্তিপণের ফোনটা পেমেন্টাল গার্ডেন লেনের যে STD বুথ থেকে করা হয়েছিল, তার হদিশ মিলল কুদ্দুসকে জেরা করে। বুথের মালিক ওয়াসিম মুবারকি জানালেন, কে ফোনটা করেছিল, চিনতে পারবেন মুখ দেখলে। আদালতে চিনিয়ে দিলেন কুদ্দুসকে, ফোন করার সময় পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একলাখকেও। বুথের ‘কল রোল’ বাজেয়াপ্ত করা হল, যা নিশ্চিত প্রমাণ করল হাদিসের ফ্যাক্টরিতে ১৩ অগস্ট সোয়া তিনটের ফোন কল।
রিপন স্ট্রিট এলাকায় বা আশেপাশের ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে খোঁজখবর করে সন্ধান পাওয়া গেল সেই ট্যাক্সিরও, যাতে চড়ে ট্রাঙ্কবন্দি মৃত হারুনকে নিয়ে কুদ্দুস-একলাখ রওনা দিয়েছিল হাওড়া স্টেশনে। WB-04/2052-র ড্রাইভার মহম্মদ আকবর সাক্ষ্য দিলেন আদালতে। সেই বিকেলের দুই আরোহীকে চিনিয়ে দিলেন, যারা একটা বড় ট্রাঙ্ক নিয়ে উঠেছিল গাড়িতে।
যে রিকশা করে ট্রাঙ্ক নিয়ে আগা মেহেন্দি লেন থেকে একলাখের দেদার বক্স লেনের বাড়িতে এসেছিলেন কুদ্দুস, খোঁজ মিলল তার চালকেরও। মহম্মদ সামসাদ, যার বয়ান পেশ হল আদালতে এবং যিনি দেখেই চিহ্নিত করলেন কুদ্দুসকে।
আগা মেহেন্দি লেনের যে প্রতিবেশী হারুনকে দেখেছিলেন কুদ্দুস-একলাখের সঙ্গে, দেদার বক্স লেনের যে সবজিবিক্রেতা হারুনকে টফি খাওয়াতে চেয়েছিলেন, তাঁদের বয়ানও গুরুত্বপূর্ণ পারিপার্শ্বিক প্রমাণ হিসেবে জায়গা পেল চার্জশিটে।
কফিনে শেষ পেরেক ঠোকার কাজটা বাকি ছিল। সম্পূর্ণ হল হারুনের প্রাণের বন্ধু ছোট্ট সাব্বির রহমানের বয়ানে। একসঙ্গে স্কুল ছুটির পর বেরনো, কুদ্দুসের ডেকে নেওয়া হারুনকে আর হারুনের খুশি মনে চলে যাওয়া। শনাক্তকরণে মুহূর্তের জন্যও দ্বিধাগ্রস্ত দেখায়নি সাব্বিরকে। সোজা আঙুল দেখিয়েছিল কুদ্দুসের দিকে, এই আঙ্কলটাই!
দীর্ঘ বিচারপর্বের পর ২০০৩ সালে দোষী সাব্যস্ত হয় কুদ্দুস-একলাখ, দণ্ডিত হয় যাবজ্জীবন কারাবাসে। উচ্চ আদালতে মুক্তির আবেদন অগ্রাহ্য হয়।
‘The Murder Room’, অন্যতম সেরা উপন্যাস ফিলিস ডরোথি জেমসের। যে প্রখ্যাত ব্রিটিশ গোয়েন্দাকাহিনি লেখিকা পিডি জেমস নামেই পরিচিত পাঠকদের কাছে। উপন্যাসটিতে লিখেছিলেন, “All the motives for murder are covered by four Ls: Love, Lust, Lucre and Loathing.”
ঠিকই। খুনের নেপথ্যে ওই চারটে কারণই থাকে শেষ বিচারে। এক, প্রেম। দুই, কামনা বা যৌন-ঈর্ষা। তিন, অর্থলোভ। চার, তীব্র রাগ-ঘৃণা-বিদ্বেষ। হারুন শিকার হয়েছিল তালিকায় চার নম্বর অনুভূতির।
কী বিচিত্র এই দ্বেষ!
১.০৯ মধ্যরাতের কিড স্ট্রিটে
[রমজান আলি হত্যামামলা
তদন্তকারী অফিসার মহম্মদ আক্রম]
কোথায় : লালবাজার কন্ট্রোল রুম।
কবে : ২০ ডিসেম্বর, ১৯৯৪।
কখন : রাত পৌনে দুটো।
ফোন বাজল ঝনঝন। রাতের শিফটের অফিসার তুললেন।
—দেরি হচ্ছে কেন? ওসি পার্ক স্ট্রিট বলছি। ফোর্স পাঠান।
—বেরিয়ে গেছে একটু আগে। পৌঁছে যাবে।
—লোকেশন নিন। ফোর্স দরকার। অ্যাজ় আর্লি অ্যাজ় পসিবল। না হলে সামলানো যাচ্ছে না।
—রজার।
নড়েচড়ে বসে কন্ট্রোল রুম। শিফট ইনচার্জ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় আন্দাজ করেন, আজ রাতটা ঝামেলার হতে যাচ্ছে। ওয়াকিটকি হাতে নিতে যেটুকু সময়। ধাতব শব্দ ছিটকে আসে পরমুহূর্তে, ‘কন্ট্রোল রুম কলিং। হেভি রেডিয়ো ফ্লাইং স্কোয়াড টেন, লোকেশন প্লিজ়?’
—রিপ্লায়িং, অ্যাপ্রোচিং ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম।
—পৌঁছে ওসি-র কাছে রিপোর্ট করুন। ডিসি সাউথ অন ওয়ে।
সে-রাতে জমাট ঠান্ডা শহরে। এখনকার মতো চটজলদি কুড়ি-বিশের ক্রিকেটে বিশ্বাসী ছিল না তখনকার পৌষ-মাঘ। ঠান্ডা শীতের রাতে লেপের আদরের ওম সহজে ক্রিজ় ছাড়ত না সে-সময়। রাস্তায় বেরলে ফুল সোয়েটার বা শাল না হলেই নয়।
বাড়তি ফোর্স যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছল, গলদঘর্ম স্থানীয় পুলিশ। শ’তিনেক লোকের কৌতূহলী দঙ্গল গেটের বাইরে। ঢুকতে চায় ভিতরে। আটকাচ্ছে পুলিশ, কী করে ওভাবে আমজনতাকে ঢুকতে দেওয়া যায় ভিআইপি এলাকায়? খুনের ব্যাপারটা জানাজানি হয়েছে কিছুক্ষণ হল, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা আসছেন, কলকাতা পুলিশের একাধিক আইপিএস অফিসার পৌঁছে গিয়েছেন। তাবড় তাবড় রাজনৈতিক নেতাদেরও গাড়ি ঢুকছে একের পর এক। লাল বাতির ছড়াছড়ি।
ভাগ্যিস গুচ্ছের টিভি চ্যানেল ছিল না তখন। থাকলে অবস্থা আরও সঙ্গিন হত। ক্যামেরা আর বুমের দাপটে নতুন সমস্যা তৈরি হত, স্পট থেকে মিনিটে-সেকেন্ডে-মাইক্রোসেকেন্ডে ‘ব্রেকিং নিউজ়’ আর এক্সক্লুসিভের ইঁদুরদৌড় সামলাতে ঘাম ছুটে যেত পুলিশের। তবু, সেই মূলত দূরদর্শন-শাসিত সময়েও সাংবাদিকদের জটলা নেহাত কম নয় রাতবিরেতে।
কোনওভাবে ভিড়ভাট্টা সামলে বছর পঁয়ত্রিশের শোকস্তব্ধ সদ্য-স্বামীহারাকে যখন ধরে ধরে গেটের দিকে আনছেন পরিচিত-পরিজনেরা, ঘড়ির কাঁটা তিনটের চৌকাঠ পেরিয়ে গিয়েছে। ঘটনার আকস্মিকতায় নির্বাক মহিলা তখন প্রায় চলচ্ছক্তিহীন।
পুলিশের তখন অনেক কাজ বাকি। ঘটনাস্থলের পুঙ্খানুপুঙ্খ স্কেচ ম্যাপ বানানো, কাদের রাতেই জিজ্ঞাসাবাদ প্রয়োজন তার তালিকা তৈরি করা, ফরেনসিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করা যত দ্রুত সম্ভব, সিজ়ার লিস্টের লেখালেখি, মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো সকাল হলেই, যাতে পরীক্ষার পর সম্ভাব্য রিপোর্টের প্রাথমিক আন্দাজ পাওয়া যায় সন্ধের আগেই। এবং, স্বামীহত্যার সাক্ষী থাকা স্ত্রীর বয়ান নিয়ে FIR নথিভুক্ত করা।
সাংবাদিকদের ব্যস্ততাও কম নয় তখন। লেট সিটির এডিশনে খবরটা ধরাতেই হবে, যে করে হোক। ফ্রন্ট পেজ় নিউজ়, নিশ্চিত।
পার্ক স্ট্রিট থানার ওসি-র চেম্বারে বসানো হয়েছে মহিলাকে। পৌনে চারটে বাজে প্রায়, একটু পরেই রাত হাঁটা দেবে ভোরের দিকে। যথাসাধ্য সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করছেন মহিলা পুলিশকর্মীরা। ডিসি ডিডি স্বয়ং থানায় উপস্থিত। অনেক সাধ্যসাধনার পর দুটি বাক্য বেরল দৃশ্যতই বিধ্বস্ত মহিলার মুখ থেকে, ‘ম্যায় তো বিলকুল আকেলি হো গয়ি… লাইফ বরবাদ হো গয়া…’ কেঁদে ফেললেন বলতে বলতেই।
—শান্ত হন ম্যাডাম, বলুন প্লিজ়, ঠিক কী হয়েছিল।
একটু ধাতস্থ হয়ে বলতে শুরু করেন তালাত সুলতানা। উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখর থেকে নির্বাচিত ফরওয়ার্ড ব্লক বিধায়ক রমজান আলির স্ত্রী।
“কলকাতায় এলে কিড স্ট্রিটের এমএলএ হস্টেলেই উঠি আমরা। ১৩ ডিসেম্বর রমজান সাহেবের সঙ্গেই এসেছিলাম। ওঁর চিকিৎসার প্রয়োজনে। উঠেছিলাম চারতলার রুম নম্বর ৩/১০-এ। গতকাল দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ সুব্বাদিদি (রেণুলীনা সুব্বা, অল ইন্ডিয়া গোরখা লিগের প্রাক্তন বিধায়ক) এল। বলল, ‘কোনও রুম খালি নেই, তোদের ঘরে রাতটা থাকতে দিবি?’ আমি সুব্বাদিদিকে চিনতাম। আর রমজান সাহেবের সঙ্গে তো দীর্ঘদিনের পরিচয়। বললেন, ‘নিশ্চয়ই। আমাদের সঙ্গেই থেকে যান।’
লাগেজ আমাদের ঘরে রেখে সুব্বাদিদি বেরল। ফিরল ছ’টা নাগাদ। রাত সোয়া ন’টায় আবার বেরল ওষুধ কিনতে। ফেরার পর আমরা তিনজন খাওয়াদাওয়া করলাম। সুব্বাদিদি দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল। আমি আর রমজান সাহেব সোয়া দশটা–সাড়ে দশটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দরজায় ঠক ঠক আওয়াজ শুনলাম, রাত সাড়ে এগারোটা হবে তখন। আমার আর রমজান সাহেবের ঘুম ভেঙে গেল। সুব্বাদিদির খুব গাঢ় ঘুম, জাগেনি। রমজান সাহেব বললেন, ‘বোধহয় মতিন, খুলে দাও। কিছু দরকার আছে হয়তো।’
মতিন ফরওয়ার্ড ব্লকের সর্বক্ষণের কর্মী। ও আর আলম রুম নম্বর ১/৮ –এ ছিল। খুলে দিলাম দরজা। বাইরে উঁকি দিয়ে দেখলাম, কই, কেউ তো নেই করিডরে! তা হলে কি ঘুমের ঘোরে ভুল শুনলাম আমরা? রমজান সাহেব বললেন, ‘দরজাটা খুলেই রাখ। মতিনই হবে। পার্টির কাজ নিয়ে কিছু আলোচনা ছিল। সে জন্যই এসেছিল নিশ্চয়ই। দরজা খুলতে দেরি হওয়ায় চলে গিয়েছে। ভেবেছে, ঘুমিয়ে পড়েছি।’
দরজা খুলে রেখেই আমি ঘরের লাগোয়া বারান্দায় গেলাম। ভাবলাম, উঠেই যখন পড়েছি, বাসনকোসনগুলো ধুয়ে রাখি। বাসন গুছোচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন মুখ চেপে ধরল। দেখি, দু’জন লোক, হাতে পিস্তল। গলায় ওটা ঠেকিয়ে কম্বল দিয়ে মুখচাপা দিয়ে হাত-পা বাঁধল কাপড় দিয়ে। টানতে টানতে নিয়ে গেল ভিতরে। দেখলাম আরও দু’জন ঢুকে পড়েছে ঘরে। আমি তখন ভয়ে প্রায় আধমরা। সুব্বাদিদি ততক্ষণে জেগে গিয়েছে টানাহ্যাঁচড়ার শব্দে। রমজান সাহেবও। ওরা সুব্বাদিদিরও মুখ-হাত-পা বাঁধল। ভয় দেখাল, শব্দ করলে জানে মেরে দেবে।
আলনায় থাকা আমার হলুদ শাড়ি দিয়ে রমজান সাহেবের গলায় পেঁচিয়ে ধরল একজন। আমি বাধা দিতে গেলে একজন সজোরে লাথি মারল পেটে, গালি দিল অকথ্য ভাষায়, ‘শালি হারামজাদি।’ রমজান সাহেব যখন ছটফট করছিলেন, ওরা বলছিল, ‘১০ তারিখে মিটিং, না? মজা দেখাব।’
আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করল, ‘টাকা কই?’ তারপর সুটকেসের উপর রাখা মানিব্যাগ থেকে যা টাকাপয়সা ছিল, নিয়ে নিল। ওরা আধঘণ্টা মতো ছিল। বারবার ভয় দেখাচ্ছিল, গুলি করে মেরে দেওয়ার।
ওরা চলে যাওয়ার পর ঘষটে ঘষটে আমি আর সুব্বাদিদি ইন্টারকমের কাছে গেলাম। রমজান সাহেবের কোনও সাড়াশব্দ পাচ্ছিলাম না। নিথর হয়ে পড়ে ছিলেন। খুব ভয় করছিল আমার।
কোনওভাবে আমি আর সুব্বাদিদি অনেক চেষ্টা করে আমার হাতের বাঁধনটা খুলতে পারলাম। ফোন করলাম মতিনের ঘরে। মতিন আর আলম দৌড়ে এল। আমাদের বাঁধন খুলে দিল। রমজান সাহেবের তখনও কোনও সাড়াশব্দ নেই। মতিন ওঁর গলার ফাঁস খুলে দিল। নাড়ি টিপে দেখল কিছুক্ষণ, নাকের কাছে হাত রাখল। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছিল তখন। মতিন ছলছল চোখে বলল, ‘রমজান ভাই আর নেই!’
পুরো ব্যাপারটা আমার চোখের সামনে ঘটল স্যার… ওদের দেখলে চিনতে পারব, খুঁজে বের করে শাস্তি দিন…..।”
ফের কেঁদে ফেললেন তালাত।
একটানা এতক্ষণ কথা বলে হাঁপাচ্ছেন তখন। তালাতকে জলের গ্লাস এগিয়ে দিলেন ডিসি ডিডি, ‘নিন ম্যাডাম, আপনার একটু বিশ্রাম দরকার। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব খুনিদের ধরতে, কথা দিচ্ছি।’
এ মামলার কথা অনেকেরই মনে থাকার কথা। জওহরলাল নেহরু রোড ধরে দক্ষিণ দিকে এগোলে পার্ক স্ট্রিটের একটু আগেই বাঁ হাতে কিড স্ট্রিট। রাস্তা ধরে সামান্য হাঁটলেই ডান দিকে এমএলএ হস্টেল। গ্রিলের উঁচু গেট, সামনে সর্বক্ষণের পুলিশি প্রহরা। ‘বিধানসভা সদস্য আবাস বিভাগ’-এর গ্লো সাইনবোর্ড চোখ এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই।
নিরাপত্তা যেখানে নিশ্ছিদ্র থাকার কথা, সেখানেই মাঝরাতে খুন হয়ে গেলেন এক বিধায়ক। তুমুল হইচই হওয়ার কথা। হলও। পুলিশের বাপবাপান্ত করার এমন পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা মিডিয়া হাতছাড়া করে না সাধারণত। বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো-র কটাক্ষ নানা রকমফেরে আক্রান্ত করল আমাদের। উত্তাপ যথানিয়মে বাড়ল রাজ্য-রাজনীতিরও।
খুনিদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার না হলে বাংলা বন্ধের হুমকি দিল ফরওয়ার্ড ব্লক। লালবাজারে গঠিত হল দুটি বিশেষ দল। সরাসরি তত্ত্বাবধানে থাকলেন উচ্চপদস্থ কর্তারা। ঘটনার দু’দিনের মধ্যেই মামলার তদন্তভার প্রত্যাশিতভাবেই বর্তাল গোয়েন্দা বিভাগের উপর। তদন্তকারী অফিসার হিসেবে নিযুক্ত হলেন হোমিসাইড শাখার তৎকালীন ইনস্পেকটর মহম্মদ আক্রম, যিনি চাকরিজীবনের শেষে অবসর নিয়েছিলেন কলকাতা সশস্ত্র পুলিশের অষ্টম ব্যাটালিয়নের ডেপুটি কমিশনার হিসেবে।
বিধানসভা সদস্য আবাস
মহম্মদ রমজান আলি হত্যা মামলা। পার্ক স্ট্রিট থানা, কেস নম্বর ৮২৫, তারিখ ২০/১২/৯৪। ধারা ৩০২/৩৪/৩৯৪/৩৯৭ আইপিসি। খুন, একই উদ্দেশ্যে একাধিকের সম্মিলিত পরিকল্পনা, লুঠের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে খুন বা গুরুতর আঘাতের চেষ্টা।
তদন্ত শুরু হল প্রথাগত বিধিনিয়মে। ময়নাতদন্তে কী পাওয়া যাবে, জানাই ছিল। শ্বাসরোধ করে খুন, ‘manual strangulation’।
রুম নম্বর ৩/১০-এ ঢুকেই একটা দশ ফুট বাই আট ফুট মতো জায়গা। মোটা পরদা টাঙানো রয়েছে সামনে। যা পেরলে মূল ঘর। পরদার ভিতর থেকে বাইরেটা দেখা যায় না, বাইরে থেকে ভিতরটাও।
যে ঘরে রমজান আলিকে হত্যা করা হয়েছিল
তন্নতন্ন করে খুঁজেও মিলল না ‘ডেভেলপ’ করার যোগ্য হাত বা পায়ের ছাপ। বেশ কিছু টুকিটাকি জিনিস বাজেয়াপ্ত করা হল বটে, কিন্তু সেসব নিয়মরক্ষার। ঘেঁটেঘুঁটেও নির্ণায়ক কিছু পাওয়া গেল না। তালাত বলেছিলেন, খুনিদের দেখে চিনতে পারবেন। ছবি আঁকানো হল বর্ণনা অনুযায়ী। ছড়িয়ে দেওয়া হল সোর্সদের মধ্যে, বিভিন্ন থানায়। লাভ হল না।
সূত্র, সে যতই তুচ্ছ হোক, পেলে তবেই না পরের ধাপ! হস্টেলের কর্মী-আবাসিক বা সেদিনের ‘ভিজিটর’-দের বিস্তারিত জেরা করেও অধরাই থাকল তদন্তের ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশ।
জটিল কেসে আমাদের প্ৰচলিত পদ্ধতি, তদন্তের অগ্রগতির কাটাছেঁড়া হয় নিয়মিত। গুরুত্বের বিচারে কখনও দু’-তিন দিন অন্তর, কখনও সকাল-বিকেল-সন্ধে। এ মামলা ছিল দ্বিতীয় গোত্রের, আক্ষরিক অর্থেই ঘুম ছুটে গিয়েছিল পুলিশের।
এমনই এক রিভিউ-বৈঠকের আগে তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে তাঁর সহযোগীর কথোপকথন। ঘটনার দিনতিনেক পরের কথা লিখছি।
—স্যার, তালাত সুলতানার বয়ান নিয়ে খটকা লাগছে।
—সে তো আমারও লাগছে, প্রথম দিন থেকেই।
—রাইট স্যার। রমজান দরজা খুলে রাখতে বলবেন কেন? মতিন আসেনি, জানার পরও?
তার চেয়েও বড় প্রশ্ন, মতিন তো বলছে সে ফোন পেয়েছে রাত একটার পর…
—আর খুনটা হয়েছে, তালাতের বয়ান অনুযায়ী রাত সাড়ে এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে। পোস্টমর্টেমও তা-ই বলছে |
—কারেক্ট! এতক্ষণ কী করছিলেন উনি?
—বলছেন তো, অনেক চেষ্টা করে হাতের বাঁধন খুলেছিলেন বলে দেরি হয়েছিল। তারপর ফোন করেছেন।
—হুঁ… ক্রিমিনাল গ্যাং হলে ফোনের লাইন কেটে দিয়ে যেত।
—হয়তো মিস করে গেছে তাড়াহুড়োয়।
—তুমিও আসল ব্যাপারটা মিস করে যাচ্ছ। বাইরে পুলিশ। নিতান্ত পরিচিতের সঙ্গে কেউ ঢুকলে তবেই রেজিস্টারে লেখা হয় না। চার জন অপরিচিত ঢুকে পড়বে এমএলএ হস্টেলে, কেউ খেয়াল করবে না? আর যদি এক এক করে ঢুকেও পড়ে কোনওভাবে, পুলিশ, রিসেপশন, সবার চোখ এড়িয়ে গেল?
—হয়তো সেন্ট্রি কনস্টেবলের ঝিমুনি এসে গিয়েছিল। শীতের রাত, সেই সুযোগে টুক করে…
—তালাত বলেছেন, সাড়ে এগারোটায় দরজায় টোকা। অন্তত তার পৌনে এক ঘণ্টা আগে সেন্ট্রি চেঞ্জ হয়। ডিউটি ধরেই কেউ ঝিমোবে না। রাত দুটো-আড়াইটা হলে তবু মানা যায়…
—মহিলা বলছেন, লোকগুলোকে দেখলে চিনতে পারবেন। স্পেশিফিক ডিটেলস দিচ্ছেন চেহারার। অথচ লাইট অফ ছিল। কী করে দেখলেন এত?
—হুঁ… ওটা তো সবচেয়ে বড় কন্ট্রাডিকশন…
—তালাতকে অ্যারেস্ট করলে হয় না? শিয়োর কিছু লুকোচ্ছেন। আর রেণুলীনাও কিছু দেখলেন না, এটাও কেমন যেন…
—গ্রেফতার করা যায়… কিন্তু রিস্ক আছে। প্রমাণ ছাড়া কমপ্লেনান্টকে ওভাবে.. অবশ্য আর একবার ইন্টারোগেট করাই যায়। ডিসি-কে বলব ভাবছি আজ।
—বলুন স্যার, এই প্রেশার আর নেওয়া যাচ্ছে না। পলিটিক্যাল মার্ডার বলে বাজার গরম করছে কাগজগুলো। আর তালাত তো ফিরে গেছেন কিষাণগঞ্জে গতকাল।
—এভাবে পলিটিক্যাল মার্ডার হয়? কত জায়গা আছে মার্ডার করার। এমএলএ ছিলেন উনি। জনসংযোগ করতে হত, মিটিং-মিছিল করতে হত। রাজনৈতিক খুন করতে এমএলএ হস্টেলের মতো সিকিয়োর জায়গায় চারজন দল বেঁধে আসবে মার্ডার করতে? হয় কখনও?
—ওই জন্যই তো আরও সন্দেহ। ডেলিবারেটলি মিসলিড করছেন তালাত। আর ভেবে লাভ নেই স্যার, ডিসি-কে বলুন।
বলা হল, আলোচনা হল বিস্তর। প্রমাণ ছাড়া আটক করাতেও সমালোচনার ঝুঁকি প্রচুর। কিন্তু তালাতের বয়ানে অসংগতির আধিক্য এতটাই, হিসেবে গরমিল এতটাই, ঝুঁকি নেওয়া ছাড়া উপায়ও ছিল না। আদালত থেকে ওয়ারেন্ট বের করা হল তালাতের নামে। ডিসি ডিডি-র নেতৃত্বে ২৪ ডিসেম্বর বিহার রওনা দিল দল। কিষাণগঞ্জের বাহাদুরপুরের বাড়ি থেকে তালাতকে গ্রেফতার করে কলকাতায় আনা হল ২৬ ডিসেম্বর।
প্রশ্নমালা তৈরিই ছিল। অথচ কাজেই লাগল না তেমন। মিনিট দশেক জেরার পর তালাত নিজেই বললেন, ‘মিথ্যে বলেছিলাম। খুনটা রবি করেছিল। রমজান সাহেবের কনফিডেন্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট।’
—করল কেন?
—সেটা আদালতে বলব। আপনাদের নয়।
—আদালতে স্বীকারোক্তি দেবেন?
—অবশ্যই, ওখানেই দেব। আপনারা ব্যবস্থা করুন।
—সে না হয় করব। কিন্তু শুরুতে মিথ্যে বলেছিলেন কেন? রবির সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?
—বললাম তো, যা বলার আদালতেই বলব। রবি আমাকে দিদি বলে ডাকত। খুনের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই।
নির্দিষ্ট দিনে তালাত আদালতে স্বীকারোক্তি দিলেন। ‘যাহা বলিব সত্যি বলিব, সত্য বই মিথ্যা বলিব না’-র পর কী সেই স্বীকারোক্তি? তুলে দিলাম হুবহু।
“আমার এই খুনের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নেই। আমি সাধারণ গৃহবধূ। দুই মেয়ে, এক ছেলে। গত মে মাসের পনেরো তারিখে পুরসভা নির্বাচন ছিল উত্তর দিনাজপুরে। তার আগের রাতে, ১৪ মে, ইসলামপুরের হোগলবাড়িতে একটা রাজনৈতিক মারামারি হয়। রমজান সাহেব আহত হন। রবি ছিল ওঁর পিএ। সবসময় সঙ্গে সঙ্গে থাকত। রমজান সাহেবকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়, ভরতি করা হয় ক্যালকাটা হসপিটালে। সেখানে এবং তারপর এমএলএ হস্টেলে আমি প্রাণপণ শুশ্রূষা করি স্বামীর। রবিও সাহায্য করেছিল খুব। ওই সময় রবির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়, অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ি আমরা। রমজান সাহেব আমার প্রতি উদাসীন ছিলেন, ভাল ব্যবহার করতেন না।
আমরা কিষাণগঞ্জের বাড়িতে তখন। ফিরে গিয়েছি চিকিৎসার পর। একদিন আমাকে আর রবিকে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় দেখে ফেলেন আমার স্বামী। রবির সামনেই অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেন আমাকে। রবিকে ছাড়িয়ে দেন কাজ থেকে। সেই থেকেই রবির আক্রোশ রমজান সাহেবের উপর। আমি অবশ্য ভুল বুঝতে পেরেছিলাম। কোনও সম্পর্ক সেই থেকে রাখিনি রবির সঙ্গে।
আবার বলছি, আমি খুন করিনি। কোনও সম্পর্ক নেই খুনের সঙ্গে। খুন রবি করেছে।
২০ তারিখ রাতে সাড়ে দশটা নাগাদ আমি, সুব্বাদিদি আর এমএলএ সাহেব ঘরে ছিলাম। সুব্বাদিদি ঘুমিয়ে পড়েছিল। রমজান সাহেবের চোখে ড্রপ দেওয়ার পর আমি মেঝেতে শতরঞ্চি পেতে শুয়েছিলাম। দুটো আলাদা খাটে আমার স্বামী আর সুব্বাদিদি শুয়ে ছিল। ঘরের লাইট অফ করা ছিল। দরজা খোলা ছিল।
হঠাৎ রবি দরজা ঠেলে পরদা সরিয়ে ঢুকল ঘরে। বলল, ‘কাকুর (এই নামেই ডাকত ও রমজান সাহেবকে) শরীর কেমন দেখতে এসেছি।’ রবিকে দেখেই ভীষণ রেগে গেলেন রমজান সাহেব। খুব গালাগালি করলেন আমাকে, বললেন, ‘তোমার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করতেই এসেছে হারামজাদা।’ রবিও ক্ষিপ্ত হয়ে বলল, ‘আপনি দিদির জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছেন।’ বলেই ঝাঁপিয়ে পড়ল রমজান সাহেবের উপর। আমি আটকানোর চেষ্টা করলাম, হাতেপায়ে ধরলাম। আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল রবি। আমি জ্ঞান হারালাম।
কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরলে দেখি, আমি সুব্বাদিদির খাটে শুয়ে। রমজান সাহেবের শার্ট আর গেঞ্জি দিয়ে আমার মুখ বাঁধা। সুব্বাদিদির মুখ বাঁধা ওঁর লাল শাল দিয়ে। এমএলএ সাহেব নিজের খাটে। গলায় শাড়ির ফাঁস দেওয়া। এর বেশি কিছু জানি না।
আমার হার্টের সমস্যা আছে। কিন্তু রমজান সাহেব কখনও আমার অসুখের ব্যাপারে যত্ন নেননি। তবু আমি ওঁর সেবাযত্নে কোনওদিন ত্রুটি রাখিনি। এবারও কলকাতায় আসা ওঁর চিকিৎসার জন্যই।”
ম্যাজিস্ট্রেট সব শুনে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘পুলিশের কাছে মিথ্যে বলেছিলেন কেন?’
তালাত সোজাসাপটা উত্তর দিলেন, ‘ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। তা ছাড়া রবি শাস্তি পাক, এটা চাইনি। ওকে ভালবেসেছিলাম আমি। পরে মনে হল, সত্যিটা না বললে অন্যায় হবে।’
যাক, তা হলে কিনারা তো হল শেষমেশ! — এমনই প্রতিক্রিয়া সাধারণত আমাদের হয় আদালতে স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি দিতে অভিযুক্ত রাজি হলে। এ যাত্রায়ও প্রাথমিকভাবে তেমনটাই ভেবেছিল পুলিশ। সত্যিটা অন্তত এবার জানা যাবে।
ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৬৪ ধারায় নথিবদ্ধ হওয়া স্বীকারোক্তির (Judicial Confession) কপি যখন হাতে এল, মাথায় হাত গোয়েন্দাদের। স্বস্তি তো দূরের কথা, বরং আরও অস্বস্তির গ্রাসে। এটা কীরকম হল?
FIR–এ যা তালাত বলেছিলেন, তার সঙ্গে বিন্দুমাত্র মিল নেই। এবং এই অমিলের থেকেও বড় কথা, আদালতে দেওয়া বয়ানেও অজস্র অসংগতি। রাত এগারোটায় কেন দরজা খুলে রাখলেন? ব্যাখ্যা নেই। এতদিন পরে রবি হঠাৎ কেন ‘কাকু’–র শরীরের খোঁজ নিতে প্রায় মাঝরাতে এমএলএ হস্টেলে চলে এল? মতিনের উল্লেখ কোথায় নয়া স্বীকারোক্তিতে? নেই। তালাত বলছেন, পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়েছিলেন। ঘটনার পরদিন প্রাথমিক চিকিৎসার সময় শরীরের কোথাও দৃশ্যমান আঘাত ছিল না, মাথাতেও নয়। একমত হলেন গোয়েন্দারা, ইনি কঠিন মহিলা। হয় মিথ্যে, নয় অর্ধসত্য বলছেন।
সিদ্ধান্ত হল, রবিকে তো আগে ধরা হোক। জেরা করলেই ‘দুধ কা দুধ, পানি কা পানি’ হয়ে যাবে। রবি শিকদার, বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। ধরা হল নদিয়ার বাড়ি থেকে, নিয়ে আসা হল কলকাতায়।
এরপর যা ঘটল, তার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না পোড়খাওয়া গোয়েন্দারাও। জানা গেল, রবি কিছুদিন গাড়ি চালিয়েছিলেন রমজানের। কাজ করেছিলেন ব্যক্তিগত সহায়ক হিসেবেও। বেশ কয়েক মাস আগে অন্য চালক নিয়োগ করেন রমজান। সেই থেকে নদিয়ার বাড়িতেই থাকেন, জমিজমা দেখাশোনা করেন। চাকরি যাওয়ার পর তালাতের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই, দেখাও হয়নি কখনও। রবি স্পষ্ট বললেন, তালাতকে ‘দিদি’ বলে ডাকতেন, প্রশ্ন নেই দূরতম কোনও অবৈধ সম্পর্কের। আরও জানালেন জোর গলায়, কলকাতায় শেষ এসেছেন মাসছয়েক আগে। ঘটনার দিন তিনি নদিয়াতেই ছিলেন।
রবিকে নিয়ে পুলিশের বিশেষ টিম রওনা হয়ে গেল নদিয়ায়। খোঁজখবর-জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ নিশ্চিত হল, রবি সত্যি বলছেন। ঘটনার দিন নিজের গ্রামের বাড়িতেই ছিলেন। অসংখ্য সাক্ষী রয়েছে। আদালতে রবির জামিনের আবেদনের বিরোধিতা করল না পুলিশ। রেহাই পেলেন নির্দোষ যুবক।
এদিকে কাগজে ফলাও করে প্রচার হয়েছে রবি ধরা পড়ার পর থেকে, চর্চা হয়েছে তালাতের স্বীকারোক্তি নিয়ে। ‘স্ত্রীর প্রাক্তন প্রেমিকের রোষেই খুন রমজান’ শীর্ষক খবর বেরিয়েছে সর্বত্র। রবির জামিনের পর আর-এক প্রস্থ নিন্দেমন্দ সহ্য করতে হল আমাদের।
অতঃকিম? লালবাজার ঠিক করল, শূন্য থেকে শুরু করা ছাড়া উপায় নেই। মূলত তিনটে সিদ্ধান্ত হল।
এক, আবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে সেই রাতে হস্টেলে থাকা সমস্ত আবাসিক-কর্মীদের, ঘটনাস্থলের এক কিলোমিটারের মধ্যে সমস্ত দোকানপাটের কর্মচারীদেরও। কেউ কিছু যদি মনে করতে পারেন, যা খেয়াল করেননি প্রথম বারের জেরায়।
দুই, এলাকার দু’-তিন কিলোমিটারের মধ্যে সমস্ত পিসিও বুথ চষে ফেলতে হবে। ঘটনার অন্তত কুড়ি দিন আগে থেকে খুনের দিন পর্যন্ত ফোনের রেকর্ড পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এমএলএ হস্টেলে বাইরে থেকে কী কী ফোন এসেছিল কখন, রুম নম্বর ৩/১০-এ তো বটেই, অন্য সব রুমেও, জানতে হবে।
তিন, টিম পাঠানো হবে উত্তর দিনাজপুরে এবং কিষাণগঞ্জে। পার্টিকর্মীদের নানাভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও মুখ খুলছেন না কেউ। স্থানীয় স্তরে সোর্স লাগিয়ে খোঁজখবর নিতে হবে রমজানের পারিবারিক ব্যাপারে। বিষয়সম্পত্তি নিয়ে কোনও বিবাদ ছিল কি না, মৃত্যুতে রাজনৈতিক ভাবে কেউ লাভবান হতে পারত কি না, রমজান-তালাতের সম্পর্কে কতটা টানাপোড়েন ছিল ইত্যাদি।
ত্রিমুখী স্ট্র্যাটেজিতে সর্বাত্মক ঝাঁপাল লালবাজার। ফলও মিলল পরিশ্রমের, ধৈর্যের, অধ্যবসায়ের।
তদন্তকারী অফিসার মহম্মদ আক্রম রোজ নিয়ম করে দশ-বারোটা পিসিও বুথে ঘুরে ঘুরে কললিস্ট ঘাঁটতে শুরু করলেন। প্রথম কিনারাসূত্র এল সেখান থেকেই।
সেদিন সন্ধে হয়ে এসেছে প্রায়। জানুয়ারির শেষাশেষি। সারাদিন টো টো করে ঘুরেছেন আক্রম। শরীরে-মনে ‘ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু’-র রিংটোন বাজতে শুরু করেছে। ঠিক করলেন, আর গোটা তিনেক বুথ ঘুরে আজকের মতো দাঁড়ি টানবেন।
৩সি চৌরঙ্গি লেন। ছোট পিসিও বুথ, মালিক রঞ্জিত দাস। আদর-আপ্যায়ন করে বসালেন আক্রমকে, চা এল। কললিস্ট খুঁজতে খুঁজতেই খুচরো এ-কথা সে-কথার মাঝে রঞ্জিত বললেন, ‘স্যার, আপনারা তো সব ক’টা বুথ ঘুরছেন ক’দিন ধরে। ওই এমএলএ মার্ডারের ব্যাপারে, না?’
—হুঁ!
—স্যার, অভয় দেন তো একটা কথা বলি?
আক্রম চোখ তুলে তাকালেন। দৃষ্টিতে খুব একটা কৌতূহল আছে, এমনটা বলা যায় না।
গলার স্বর প্রায় খাদে নামিয়ে আনেন রঞ্জিত।
—স্যার, ম্যাডাম আমার বুথে প্রায়ই আসতেন ফোন করতে। ভাল আলাপ আছে আমার সঙ্গে।
—কোন ম্যাডাম?
—এমএলএ সাহেবের মিসেস।
আক্রম আবার চোখ তুললেন ফোন নম্বরের তালিকা থেকে। দৃষ্টি বদলে গিয়েছে এখন, উঠে পড়েছেন চেয়ার ছেড়ে। ক্লান্তি- শ্রান্তি উধাও।
—কোথায় করতেন ফোন?
—এসটিডি কল স্যার। দিল্লিতে।
—কোন নম্বর? শেষ কবে করেছেন?
—দশ মিনিট বসুন স্যার, বের করে দিচ্ছি। শেষ এসেছিলেন বোধহয় মাসখানেক আগে। স্পষ্ট মনে আছে। আর একবার চা বলি স্যার?
চা কেন, স্বর্গের অমৃতসুধা এনে দিলেও তাতে তখন আর রুচি নেই আক্রমের। সম্ভাব্য সূত্রের আভাস পেলে তদন্তকারী অফিসারের যা হয়, মনের তখন সেই অবস্থা। শিরা-ধমনীতে একে অন্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে উত্তেজনা-উৎকণ্ঠা-ঔৎসুক্য।
২০ অক্টোবর থেকে ১৫ ডিসেম্বর, বারোবার তালাত ফোন করেছিলেন দিল্লিতে। নম্বর ০১১-৭৩৮৬২৪। কথোপকথনের সময়সীমা কখনও তিন-চার মিনিট, কখনও আট-দশ। ওই বুথ থেকেই ফোন ঘোরালেন আক্রম। নম্বরটা দিল্লির একটা ব্যবসায়িক সংস্থার, নাম ‘Mumbai Trading & Co’। মালিকের নাম কলিম খান। যাঁকে জিজ্ঞাসা করা হল কর্মচারীদের ব্যাপারে। বাংলা বা বিহারের কেউ আছে? এমন কি কেউ আছে যে কুড়ি তারিখ কাজে আসেনি?
—হাঁ, বাঙ্গাল সে এক হ্যায়। নুরুল, নুরুল ইসলাম। ষোলা তারিখ সে ছুট্টি লিয়া থা। লওট কে নেহি আয়া। কোই গড়বড় হ্যায় কেয়া?
এক মুহূর্ত দেরি করলেন না আক্রম। গাড়ি ছোটালেন লালবাজারে। ঝটিতি মিটিং সারলেন ডিসি ডিডি। সেই রাতেরই ট্রেন ধরতে রওনা হয়ে গেলেন অফিসারদের একটি দল। গন্তব্য দিল্লি।
পাশাপাশি ঠিক হল, যদি নুরুলই খুনি হয়, আর দিল্লি থেকে এসেই যদি খুনটা করে থাকে, আশেপাশের হোটেলে ওঠার একটা সম্ভাবনা রয়েছে। আজ রাতেই হানা দিতে হবে দক্ষিণ ও মধ্য কলকাতার সমস্ত হোটেল-ধর্মশালায়। নুরুল ইসলাম বা অন্য কোনও নামে ১৬/১৭ তারিখ থেকে ২০ তারিখের মধ্যে কেউ উঠেছিল কি না, খোঁজ নিতে হবে।
বেশি পরিশ্রমের দরকার পড়ল না। ঘণ্টা তিনেকের ছোটাছুটির পরই এমএলএ হস্টেল থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বের খাজা হাবিব হোটেলের রেজিস্টারে পাওয়া গেল নুরুল ইসলামের নাম। উঠেছিলেন ১৯ তারিখ সকালে, লিখেছিলেন ২২ তারিখ অবধি থাকবেন। কিন্তু ২০ তারিখ রাতেই টাকাপয়সা মিটিয়ে দিয়ে দশটা নাগাদ বেরিয়ে যান।
পরদিন সকালেই আরও প্রমাণ মিলল। সে-রাতে হস্টেলের ভিজিটার্স রেজিস্টারে যাঁদের নাম ছিল, তাঁদের সবাইকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। দ্বিতীয় দফায় আর একটি দল জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছিল বেশ কয়েকদিন ধরে। জেরায় মনজুর আলম বলে একজন অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিলেন, যেটা প্রথমবার বলেননি।
“রমজান সাহেব আমাদের এলাকার বিধায়ক। আমার বাড়ি চাকুলিয়া থানা এলাকায়। রমজান সাহেবের আদি বাড়ি কিষাণগঞ্জে, কিন্তু ওঁর আমাদের গ্রামের কাছেও একটা বাড়ি ছিল। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের সঙ্গে আমাদের একটা জমিজমা সংক্রান্ত মামলা চলছিল অনেকদিন ধরে। সেই ব্যাপারে সাহায্য চাইতে বেশ কয়েকবার গিয়েছি এমএলএ সাহেবের বাড়ি। ওখানে নুরুলকে দেখেছি। রমজান সাহেবের ব্যক্তিগত সহায়ক ছিল নুরুল। ওর বাড়ি চাকুলিয়া থানারই বড়ডিহা গ্রামে। আলাপ ছিল আমার সঙ্গে।
২০ তারিখে কলকাতায় এসেছিলাম কাজে। উঠেছিলাম বেকার হস্টেলে এক বন্ধুর রুমে। রাত ১০টা নাগাদ করণদিঘির বিধায়ক সাজাদ আলির সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল এমএলএ হস্টেলে। ব্যবসায়িক সমস্যার ব্যাপারে। গিয়ে দেখি, সাজাদ সাহেবের রুম (২/৭) তালাবন্ধ।
আধঘণ্টা অপেক্ষা করলাম। সাজাদ ভাই এলেন না। ভাবলাম, রমজান ভাইয়ের রুম থেকে ঘুরে আসি একবার। জানতাম, উনি কলকাতায় এসেছেন। হস্টেলে রুম ৩/১০-এই উঠতেন চিরকাল। সিঁড়ি দিয়ে চারতলায় উঠলাম। রুমের সামনে গিয়ে দেখলাম, ভিতর থেকে বন্ধ। আলো জ্বলছে না। ভাবলাম, ঘুমিয়ে পড়েছেন। অসুস্থ মানুষ, ডিস্টার্ব করা ঠিক হবে না।
যখন লিফটের দিকে ফিরে আসছি, নুরুলকে করিডরের উলটোদিক থেকে আসতে দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী ভাই, এখানে এত রাতে?’ নুরুল বলল, রমজান সাহেবের সঙ্গে একটা দরকার আছে।”
গোয়েন্দারা মনজুরকে জিজ্ঞাসা করলেন, এসব আগে বলেননি কেন?
—স্যার, পরের দিন যখন শুনলাম, রমজানভাই খুন হয়ে গিয়েছেন, ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, সব বলতে গিয়ে যদি ঝামেলায় পড়ি, কোর্টকাছারি করতে হয়, কী দরকার?
ওদিকে রহস্যজাল পরতে পরতে খুলতে শুরু করেছে কিষাণগঞ্জের বাড়িতেও। যেখানে রমজানের পরিবারের খুঁটিনাটি তথ্যতালাশ চালাচ্ছিলেন গোয়েন্দারা। জেলার অত্যন্ত প্রভাবশালী পরিবার, কঠিন হচ্ছিল আত্মীয়-পরিজন, পাড়াপ্রতিবেশী-পার্টিসদস্যদের মুখ খোলানো। কিন্তু খবর বের করাটাই তো কাজ আমাদের। যেন তেন প্রকারেণ।
কী-কখন-কেন-কীভাবের উত্তর ধীরে, কিন্তু নিশ্চিতভাবেই এল প্রকাশ্যে।
১৯৮৯ থেকে ’৯৩, চার বছর রমজান আলির ব্যক্তিগত সহায়ক হিসেবে কাজ করেছিল নুরুল ইসলাম। ’৯১ সালে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন রমজান। ডায়াবেটিস ধরা পড়ে, ক্ষয়রোগও বাসা বাঁধতে শুরু করেছিল শরীরে। চিকিৎসার জন্য দিল্লি গেলেন, সঙ্গে তালাত আর নুরুল। রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালে বেশ কিছুদিন চিকিৎসাধীন থাকলেন রমজান এবং ক্রমে ঘনিষ্ঠতা বাড়ল তালাত-নুরুলের।
রমজান তখন পঞ্চাশোর্ধ্ব, নানা রোগভোগে জীর্ণ। তালাত সবে তিরিশ পেরিয়েছেন, নুরুলও সমবয়সি প্রায়। ঘি এবং আগুনের সহাবস্থানে যা হওয়ার, তাই হল। গভীর সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লেন দু’জনে। মানসিক, শারীরিকও। চিকিৎসার পর কিষাণগঞ্জে ফিরলেন রমজান। কিছুদিনের মধ্যেই আঁচ করতে পারলেন তালাত আর নুরুলের ব্যাপারটা। একদিন দু’জনকে ধরে ফেললেন ঘনিষ্ঠ অবস্থায়। গালাগাল-মারধোর করে তাড়িয়ে দিলেন নুরুলকে। লেখার অযোগ্য শব্দ ব্যবহার করলেন তালাতের উদ্দেশে।
নুরুল দিল্লি চলে গেলেন, চাকরি নিলেন Mumbai Trading & Co–তে। রমজান ভাবলেন, আপদ গেল। কিন্তু সম্পর্ক ততদিনে গড়িয়েছে অনেকদূর। ভৌগোলিক দূরত্বের সাধ্য ছিল না আর তাতে ইতি টানার। নিয়মিত চিঠির আদানপ্রদান চলতে থাকল তালাত-নুরুলের। সপ্তাহে অন্তত দু’বার ফোনেও প্রেমালাপ।
ভাই হাফিজ আলম সৈরানি এবং খুব ঘনিষ্ঠ কয়েকজনের কাছে তালাতের ব্যাপারে বিষোদ্গার করতেন এমএলএ সাহেব। রমজান-তালাতের পারস্পরিক অবিশ্বাস আর তিক্ততা কোন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছিল, তা বোঝা যায় দুটি নথি থেকে। প্রথমটা রমজানের ডায়েরির পাতা, যা উদ্ধার হয়েছিল কিষাণগঞ্জের বাড়ি থেকে। কিছু অংশ তুলে দিলাম।
‘আজ, ১৩/৪/৯২, বড় দুঃখের সাথে লিখছি। ভালবাসার ধারণাটাই বদলে গিয়েছে আমার।
লুকিয়ে লাভ নেই, আমার অসুস্থতার সুযোগ নিয়ে নিজের শারীরিক চাহিদা মেটাতে আমার স্ত্রী এমন একজনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে, যার সঙ্গে মাত্র কয়েক বছরের আলাপ। এই অনাচার আমাকে সহ্য করতে হচ্ছে। দিনের পর দিন। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, যখন এই সেদিন ও আমাকে বলল, প্রয়োজনে আবার বিয়ে করবে!’
দ্বিতীয়টা নুরুলকে লেখা তালাত সুলতানার একটি চিঠি, যেটা তিনি পোস্ট করেননি। এটিও উদ্ধার হয়েছিল ওই কিষাণগঞ্জের বাড়ি থেকেই। উর্দু চিঠির অংশবিশেষ রইল বঙ্গানুবাদে।
‘ডিয়ার,
আদাব।
চিঠি পেয়েছি।
এত দুঃখ পাচ্ছি এখানে যে ইচ্ছে করছে তোমার সঙ্গে দেখা করে সব দুঃখ হালকা করে নিই। লোকে ঠিকই বলে। অভীষ্টের খোঁজে আমরা এমন জায়গায় পৌঁছে যাই, যখন মনে হয় খুঁজতে খুঁজতে সব হারিয়ে ফেলেছি। ভয় হয়, তোমাকেও হারিয়ে ফেলব না তো? আমার জীবন বলতে তো তুমিই।’
ঘটনার পর আর দিল্লি ফেরেনি নুরুল। পালিয়েছিল বিহারে। জানুয়ারির শেষ থেকে পুলিশ বিহারের আনাচকানাচ চষে ফেলেছিল নুরুলের খোঁজে। একটা দল ঘাঁটি গেড়েছিল উত্তর দিনাজপুরে, অন্যটা বিহারে। মাসখানেক চোর-পুলিশ খেলার পর নুরুল ধরা পড়েছিল ফেব্রুয়ারির ২৭ তারিখে, রায়গঞ্জের শিলিগুড়ি মোড় থেকে।
জেরাতে নুরুল স্বীকার করেনি কিছু, গোয়েন্দারা অকাট্য পারিপার্শ্বিক প্রমাণ হাজির করা সত্ত্বেও। অনড় থেকেছে নিজেকে নির্দোষ ঘোষণায়, যুক্তি-তর্ক কিছুই ধোপে টিকছে না দেখেও।
রেণুলীনা সুব্বার সাক্ষ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু কে জানে কেন, উনি FIR–এ তালাতের প্রাথমিক বক্তব্যকেই ঘুরিয়েফিরিয়ে সমর্থন করে আদালতে স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন। পুলিশ বুঝেছিল, সত্য গোপন করছেন। রেণুলীনা নিজেও জানতেন নিশ্চিত, আসলে কী ঘটেছিল। কিন্তু বলেননি, হাজার প্রশ্নবাণের মুখেও নড়েননি একটুও। তালাতকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন, পরিষ্কার। কিন্তু কেন? উত্তর পাইনি আমরা। সব কিছু জানা যায় না।
দ্রুত চার্জশিট পেশের পর দীর্ঘ বিচারপর্ব চলেছিল। তীব্র বাদানুবাদের সাক্ষী থেকেছিল আদালত। তালাত-নুরুলের আইনজীবী দাবি করেছিলেন, এটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। যে যুক্তিকে গুরুত্ব দেওয়ার কারণ খুঁজে পায়নি আদালত। পারিপার্শ্বিক প্রমাণের ঠাসবুনোট বুনিয়াদ তৈরি করেছিলেন তদন্তকারী অফিসার।
খাজা হাবিব হোটেলের রেজিস্টারে খুনের আগের দিন নুরুলের হাতের লেখার সঙ্গে পুলিশি হেফাজতে থাকাকালীন সংগৃহীত ‘handwriting specimen’–এর মিলে যাওয়া। পিসিও বুথের কলকাতা-দিল্লি ফোনের খতিয়ান, বুথমালিকের শনাক্তকরণ তালাতকে। মনজুর আলমের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে নুরুলের এমএলএ হস্টেলে ঘটনার রাতে উপস্থিতি প্রমাণ হওয়া। তালাত, তদন্তে জানা গিয়েছিল, বেশ কয়েকবার নিউ মার্কেটের সাব-পোস্ট অফিস থেকে মানিঅর্ডারে টাকা পাঠিয়েছিলেন নুরুলকে। তার রসিদের প্রতিলিপি উভয়ের সম্পর্কের গভীরতা বোঝাতে আদালতে পেশ হওয়া। উত্তর দিনাজপুরে জয়শ্রী কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্টিলাইজারের
সাব-ডিস্ট্রিবিউটরশিপ গোপনে নিয়েছিলেন তালাত-নুরুল। সংশ্লিষ্ট প্রমাণ হাজির করা সেই ব্যবসায়িক অংশীদারির। এবং সর্বোপরি রমজানের ডায়েরির পাতার আক্ষেপ আর তালাতের পোস্ট-না-করা প্রেমপত্র।
নিম্ন আদালত তালাত-নুরুলকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজা শুনিয়েছিল। হাইকোর্ট যা বহাল রেখেছিল। দু’জনেই এখনও সংশোধনাগারে।
ঠিক কী ঘটেছিল সে-রাতে? নুরুল-তালাত স্বীকার করেননি, রেণুলীনা কৌশলে এড়িয়েছেন। কিন্তু এঁদের তিনজনকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা করে, সব দিক বিচার করে তদন্তকারী দলের যা নিশ্চিতভাবে মনে হয়েছিল, তা এরকম।
নুরুল কলকাতায় এসেছিলেন তালাতের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু বাইরে দেখা করায় ঝুঁকি ছিল অনেক। দু’জনে ঠিক করেছিলেন, রাতে রমজান ঘুমিয়ে পড়লে নুরুল হস্টেলের ঘরে আসবেন। রেণুলীনার রাত্রিবাসটা হিসেবের বাইরে ছিল। রাত্রি সাড়ে দশটা-পৌনে এগারোটা নাগাদ গেটের বাইরের ‘সেন্ট্রি চেঞ্জ’ হচ্ছিল। পাহারা বদলের সময় নজরদারি একটু ঢিলেঢালা থাকেই। সেই সুযোগেই চাদরমুড়ি দিয়ে ঢুকেছিল নুরুল। ‘ভিজিটার্স রেজিস্টার’-এর দায়িত্বে যিনি ছিলেন রিসেপশনে, তাঁরও নজর এড়িয়ে গিয়েছিল।
তালাত দরজা খুলে রেখেছিলেন পৌনে এগারোটার পর। রমজান আর রেণুলীনা তার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়বেন, নিশ্চিত ছিলেন। ঘুমিয়ে পড়েওছিলেন ওঁরা। এগারোটা নাগাদ সন্তর্পণে ঢুকলেন নুরুল। পরদা ঘেরা জায়গায় একান্তে দু’জনে সময় কাটানোই ছিল উদ্দেশ্য।
বাদ সাধল ফিসফিস কথার আওয়াজে রমজানের ঘুম ভেঙে যাওয়ায়। উঠে পড়লেন, গলা ছেড়ে আওয়াজ দিলেন। রমজান বুঝে ফেলেছিলেন, নুরুল এসেছে। এবং নুরুল জানত, যেখানেই পালান, পার পাবেন না। রমজান ক্ষমতাশালী লোক, ধনেপ্রাণে অতিষ্ঠ করে দেবেন জীবন। এরপর রমজানের গলায় ফাঁস দেওয়া নুরুলের। রেণুলীনার সঙ্গে তালাতকেও বেঁধে ফেলার নাট্যরূপ। নুরুল বেরিয়ে গিয়েছিল মেন গেট দিয়েই। প্রহরায় থাকা পুলিশ সন্দেহ করেনি। ভেবেছিল, ঢুকেছে যখন, বৈধভাবেই ঢুকেছে। বৈধ অতিথিকে আটকানোর কথাও নয় বেরনোর সময়।
রমজানের মৃতদেহ, গলায় ফাঁস লাগানো
রাজনীতির কোনও প্যাঁচপয়জার ছিল না রমজান-হত্যায়। খুন, কিন্তু ছক কষে নয়। সে তালাতই হন বা নুরুল, দাগি আসামি তো আর ছিলেন না। খুন-পরবর্তী-চিত্রনাট্যে ফাঁকফোকর থেকে গিয়েছিল বিস্তর। আবেগ আর আক্রোশের তাৎক্ষণিক তাড়নাই ছিল চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেপথ্যে, পোড়খাওয়া অপরাধীর স্থিরমস্তিষ্ক নয়।
সত্যের অন্বেষণই তদন্তের মূল কথা, “to ascertain the truth”। তবে সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী যে বিলাসিতা দেখাতে পারতেন, তা আমাদের, বাস্তবের সত্যসন্ধানীদের থাকে না। এক এবং অদ্বিতীয় ব্যোমকেশ উৎসাহী ছিলেন অপরাধীর মনস্তত্ত্বে, সত্য উদ্ঘাটনে। শাস্তিবিধানে তাঁর নিবিড় মনোনিবেশ বড় একটা দেখি না আমরা। অপরাধীর বাধ্যবাধকতা বিচার করে কখনও কখনও অব্যাহতি দেন সত্যিটা জানা হয়ে যাওয়ার পর, স্বজ্ঞানে মুক্তি দেন পুলিশের হাত থেকে। বিবেকের শাসনে জীবনভর যন্ত্রণা পাওয়াকেই যথেষ্ট শাস্তি মনে করেন।
বাস্তবের গোয়েন্দা রক্তমাংসের, আইনের চৌহদ্দির বাইরে যাওয়ার অধিকার তাঁর নেই। তাঁকে বাধ্যত নিরাবেগ হতে হয়। অভিযুক্তকে ধরা, সাক্ষ্যপ্রমাণ একত্রিত করা এবং আদালতে চার্জশিট দাখিল করা শাস্তিবিধান চেয়ে। অনেক অপরাধই ঘটে যায় বিচিত্র পরিস্থিতির জাঁতাকলে। তদন্তকারী অফিসার যতই নৈর্ব্যক্তিক মানসিকতায় রহস্যভেদ করুন, কখনও কখনও সহানুভূতি বা সম-অনুভূতি মননে প্রভাব ফেলেই। সেই প্রভাবের ছোঁয়াচ কাটিয়ে নির্মোহ তদন্ত কোনও কোনও ঘটনায় নেহাত সহজসাধ্য নয়।
আক্রম সাহেব কি কখনও আক্রান্ত হয়েছিলেন দ্বিধা-দ্বন্দ্বের টানাপোড়েনে, যখন তদন্ত চলছিল মামলার, যখন একটু একটু করে পরদা উঠছিল রহস্যের? ভেবেছিলেন, কোন পরিস্থিতিতে, কোন মনস্তাপে তালাত এতটা মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন? কুড়ি বছর সংসারযাপনের পর, তিন সন্তানের জন্মদাত্রী হয়েও? কে জানে?
জল্পনায় লাভও নেই বোধহয়। কথাই তো আছে, “the more you know, the more you know you don’t know.”
যত বেশি জানবে, ততই বেশি জানবে, জানা হয়নি বিশেষ।
১.১০ বয়স হয়েছিল পঁয়ত্রিশ
[বাপি সেন হত্যামামলা
তদন্তকারী অফিসার অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়]
মেরে স্বপ্নো কি রানি কব আয়েগি তু..
আয়ি রুত মস্তানি কব আয়েগি তু..
বিতি যায়ে জিন্দেগানি কব আয়েগি তু..
চলি আ.. আ তু চলি আ …
শেষ লাইনটা গাওয়া হচ্ছে কোরাসে। ট্যাক্সি থেকে মুখ বার করে এক যুবক তারস্বরে গাইছে। বলা ভাল, চেঁচাচ্ছে, আ তু চলি আ…। বিকৃত উল্লাসে গলা মেলাচ্ছে ট্যাক্সির ভিতরের বাকিরা, চলি আআআ…।
যাঁর উদ্দেশে নেশাতুর আহ্বান, মোটরসাইকেলের পিছনে বসা যুবতী, ততক্ষণে আতঙ্কের শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছেন। হাত ধরে টানার চেষ্টা করছে ট্যাক্সির জানালা থেকে এক যুবক, অশ্লীল ইঙ্গিতসহ মন্তব্য ছিটকে আসছে, হ্যাপি নিউ ইয়ার ডার্লিং! কোনওক্রমে সামলাচ্ছেন যুবতী, পুরুষসঙ্গীকে বলছেন, তাড়াতাড়ি চালাও, ভয় করছে ভীষণ।
কী করে চালাবেন তাড়াতাড়ি? সম্ভব কখনও, যখন ইচ্ছেমতো গতি বাড়িয়ে-কমিয়ে ধাওয়া করছে ট্যাক্সি মিনিট দশেক ধরে? সামনে যে রাস্তা ধু ধু ফাঁকা, এমনও নয়। ওই মাঝরাতের রাজপথে তখনও গাড়ির জটলা যথেষ্ট। মোটরসাইকেলের গতি কমিয়ে দিলে ট্যাক্সিও কমাচ্ছে, বাড়ালে দ্রুত তাল মিলিয়ে পাশে চলে আসছে। আশেপাশে পুলিশও তো কই দেখা যাচ্ছে না। যত পুলিশ আজ পার্ক স্ট্রিটে। কী করা যায়, কী করা উচিত?
সামনে ওয়েলিংটন স্কোয়ার, হিন্দ সিনেমা। এভাবে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যাবে যে-কোনও মুহূর্তে! বাধ্য হয়েই মোটরসাইকেল থামালেন চালক। হেলমেট খুললেন। ট্যাক্সিও থামল। নেমে এল পাঁচ যুবক, সবারই বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে। যুবতী দাঁড়িয়ে জড়সড়। সঙ্গী বললেন, ‘এটা কী হচ্ছে? অসভ্যতা করবেন না প্লিজ়।’
অসভ্যতা ভাবলে তো অসভ্যতা! ততক্ষণে যুবতীকে ঘিরে ফেলেছে পাঁচজন। সঙ্গী বাধা দিতে এলে বিদ্রুপ এবং ধাক্কা, ‘তুই একাই মস্তি করবি বে?’ শুরু হয়ে গিয়েছে মহিলার হাত ধরে টানাটানি। এবং পাল্লা দিয়ে খিস্তিখেউড়।
এমন চলল মিনিটখানেক। পাশ দিয়ে এরপর হুস করে বেরিয়ে গেল একটা লাল মারুতি। ব্রেক কষল মিটার পঞ্চাশেক এগিয়ে। সিনেমায় যেমন হয়। দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন এক দীর্ঘদেহী সুঠাম চেহারার যুবক। ছুটলেন পিছনে, যেখানে তখন অভিনীত হচ্ছে এক অসহায় যুবতীর অসম্মানিত হওয়ার চিত্রনাট্য।
মহিলাকে আগলে দাঁড়ালেন দীর্ঘদেহী, ‘কী হচ্ছেটা কী, ছাড়ুন ওঁকে!’
ক্ষিপ্ত উত্তর আসে, ‘তুই কে শালা ফোঁপরদালালি করার? পাতলা হয়ে যা চটপট।’
বর্ষবরণের রাত ছিল সেটা। ৩১ ডিসেম্বর, ২০০২। ঘটনা যখন ঘটছে, ঘড়ির কাঁটা অবশ্য তখন একটা পেরিয়ে গিয়েছে। ঘুরে গিয়েছে বছর। পয়লা জানুয়ারি, ২০০৩।
ফাস্ট ফরোয়ার্ডে পরের দৃশ্য। চার দিন পেরিয়ে গিয়েছে ঘটনার। ৫ জানুয়ারির রাত আটটা। হাসপাতাল চত্বর ভিড়ে থিকথিক। মিডিয়া তো রয়েইছে একঝাঁক। তার চেয়েও ঢের বেশি কলকাতা পুলিশের নানা স্তরের কর্মী-আধিকারিকরা। যাঁরা হাসপাতাল-প্রাঙ্গণকেই ঘরবাড়ি করে ফেলেছেন পয়লা জানুয়ারির দুপুর থেকে। ‘যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ’-এর আপ্তবাক্যে ভরসা রেখে।
—ডক্টর আগরওয়াল, প্লিজ়, ওকে বাঁচান। যেভাবে হোক। উই কান্ট অ্যাফোর্ড টু লুজ় হিম…। নগরপালের আর্তি ছুঁয়ে যায় প্রথিতযশা নিউরোসার্জেনকে।
—আপ্রাণ চেষ্টা করছি আমরা। নিউরোলজিক্যাল স্ট্যাটাস ভেরি পুয়োর। কোমায় চলে গিয়েছে। প্রচুর ইন্টারনাল ইনজুরি, স্কালে মাল্টিপল ফ্র্যাকচার। জানি না, কতটা সম্ভব হবে। ফিঙ্গারস ক্রসড, ট্রায়িং আওয়ার বেস্ট…। ফোন রেখে দেন ডক্টর অজয় আগরওয়াল।
Calcutta Medical Research Institute (সিএমআরআই)-এর আইসিইউ-তে চূড়ান্ত ব্যস্ততা তখন। ক্রমশ আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে পেশেন্ট। যা যা করা সম্ভব, করছেন ডাক্তাররা। হাসপাতালে ভরতি হওয়া ইস্তক রোগীর জ্ঞান ফেরেনি, ফেরার দূরতম সম্ভাবনাও ক্ষীণ হয়ে আসছে ক্রমশ। প্রহর গোনা একরকম শুরুই হয়ে গিয়েছে অবশ্যম্ভাবী পরিণতির।
সার্জেন্ট বাপি সেন হত্যা মামলা। বউবাজার থানা, কেস নম্বর ১/২০০৩। তারিখ জানুয়ারির পয়লা। ধারা, ৩০২/৩৪/৩৫৪ আইপিসি। খুনের উদ্দেশ্যে একাধিকের সম্মিলিত পরিকল্পনা, শ্লীলতাহানির উদ্দেশ্যে মহিলার উপর বলপ্রয়োগ।
এ মামলায় সে অর্থে রহস্যভেদের রোমাঞ্চ নেই, নেই একাধিক সন্দেহভাজনের মধ্য থেকে অপরাধীকে চিহ্নিত করতে মগজাস্ত্রের কুশলী প্রয়োগ। বাপি সেনের হত্যা তবু আজও কলকাতা পুলিশের ইতিহাসে সবচেয়ে চর্চিত মামলাগুলির অন্যতম। ঠিক কী ঘটেছিল, কীভাবে ঘটেছিল, জল্পনার বিষয় আজও। পনেরো বছর পরেও। শহর কলকাতাকে সে-সময় তোলপাড় করে দেওয়া এই ঘটনার প্রামাণ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ রাখা জরুরি। কেস ডায়েরির খুঁটিনাটি, আদালতে বাদী-বিবাদীর তর্কবিতর্ক এবং সর্বোপরি যাবতীয় তথ্যপ্রমাণের চুলচেরা বিশ্লেষণের পর বিচারকের রায়, ধরা থাকল ঘটনাপ্রবাহ। যা ঘটেছিল, যে ভাবে ঘটেছিল।
বেহালার পর্ণশ্রীর বাসিন্দা নারায়ণচন্দ্র সেন-রেণুকা সেনের তিন পুত্র, তিন কন্যা। নারায়ণবাবু পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অবসরপ্রাপ্ত সাব-ইনস্পেকটর। বড়ছেলে জয়দেব থাকেন সপরিবারে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের M.E.S. কোয়ার্টারে। মেজো অনুপ, ইন্ডিয়ান ব্যাংকের কর্মী। ছোটছেলে বাপি। চব্বিশ বছর বয়সে কলকাতা পুলিশে সার্জেন্ট হিসেবে যোগদান ’৯১-তে। বোনদের মধ্যে জয়শ্রী অবিবাহিতা। বাকি দুই বোন মন্দিরা আর দীপার শ্বশুরবাড়ি যথাক্রমে মহেশতলা এবং পর্ণশ্রীতে।
বাপির স্ত্রী সোমা, বিয়ে হয় ’৯২-এর জুনে। বাপি-সোমার দুই ছেলে। সোমশুভ্র বড়, ঘটনার সময় বয়স ছয়, ক্লাস ওয়ান। ছোট শঙ্খশুভ্র, হাঁটি-হাঁটি পা-পা তখন। বয়স সবে এক পেরিয়েছে দুধের শিশুর।
বাপি ছোটবেলা থেকেই ছিলেন ডাকাবুকো স্বভাবের। বাবাকে আশৈশব দেখেছেন পুলিশের চাকরিতে, স্বপ্ন লালন করতেন ভবিষ্যতে উর্দিধারী হওয়ার। খেলাধুলোয় তুমুল উৎসাহ, ভাল ফুটবল খেলতেন। টেবিলটেনিসও। ২০০২ সালে, ঘটনার সময়, টালিগঞ্জ ট্রাফিক গার্ডে কর্মরত ছিলেন। প্রতিবাদী স্বভাবের জন্য পরিচিত ছিলেন চাকরিজীবনের শুরু থেকেই। পার্ক স্ট্রিট এলাকায় এক মহিলার হার ছিনতাই করে পালানো দুষ্কৃতীকে অনেকটা ধাওয়া করে হাতেনাতে ধরেছিলেন একবার। কে জানত, ওই প্রতিবাদী স্বভাবেরই মাশুল দিতে হবে প্রাণ দিয়ে, মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে?
বাপি সেন
৩১ ডিসেম্বর, ২০০২, নিউ ইয়ার্স ইভ।
কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচিতি জরুরি ঘটনায় ঢোকার আগে। অশোক সেনগুপ্ত, বাড়ি নেতাজিনগরে। পেশায় মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, মুম্বইয়ের একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত। নাজিবুল হোসেন মোল্লা, দক্ষিণ কলকাতারই বাসিন্দা, ইনিও মেরিন ইঞ্জিনিয়ার। গৌতম মজুমদারেরও একই পেশা, থাকতেন পর্ণশ্রীতে। কানাই কুন্ডু, কলকাতা পুলিশের কনস্টেবল। বাড়ি বেহালা অঞ্চলেই।
উপরে যাঁদের নাম করলাম, অনেকদিনের পরিচিতি পরস্পরের। সকলেই মধ্যতিরিশ। বাপিও ছিলেন এই বন্ধুদলে। পর্ণশ্রী রিক্রিয়েশন ক্লাবের পাশের মাঠটা ছিল সান্ধ্য আড্ডার ঠিকানা।
সেদিন বাপির দুপুরের শিফটে ডিউটি ছিল। সোয়া আটটা নাগাদ বাড়ি ফিরে হাতমুখ ধুয়ে গেলেন ক্লাবের মাঠে। গৌতম-অশোক-নাজিবুল-কানাই তখন আড্ডা দিচ্ছেন জমিয়ে। কথায় কথায় অশোক বললেন, সঙ্গে গাড়িটা এনেছি। চল, পার্ক স্ট্রিট ঘুরে আসি রাতের দিকে। লাল মারুতি, WB-02F-4992, রওনা দিল পার্ক স্ট্রিটের উদ্দেশে। রাত কত হবে তখন? ন’টা-সোয়া ন’টা। গাড়ি একটু এগোনোর পর বাপি বললেন, তারাতলায় এক বন্ধুর বাড়ি রাত্রে যাব বলে কথা দিয়েছিলাম। একবার না গেলেই নয়। ওখান থেকে পার্ক স্ট্রিট যাওয়া যাবে।
বন্ধুর নাম সুব্রত বসু। তারাতলার কাছেই ‘নাবিকগৃহ’, মার্চেন্ট নেভির শিক্ষানবিশদের আবাসিক প্রশিক্ষণ সংস্থা। সুব্রতর বাবা সেখানে সুপারিন্টেনডেন্ট, থাকেন সরকারি কোয়ার্টারে। বাপিরা পৌঁছলেন। যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন করে সুব্রতর বাবা-মা একরকম বাধ্যই করলেন সবাইকে রাতের খাওয়াটা ওখানেই সারতে। খাওয়াদাওয়ার পর সুব্রতও সঙ্গী হলেন বাপি-গৌতম-অশোক-কানাই-নাজিবুলের। গন্তব্য পার্ক স্ট্রিট। বন্ধুদের সঙ্গে বাপি সেনের ‘The last ride together।’
বছরের শেষ রাতের পার্ক স্ট্রিট যেমন হয়। আলো আর রঙের দাঙ্গা লেগেছে যেন। কানের পরদা বিদ্রোহ করছে আওয়াজের ধাক্কায়। যতদূর চোখ যায়, ফুটপাথে কালো মাথা পিলপিল। গাড়িঘোড়াই বা কম যায় কীসে, স্রোত যেন শেষ হওয়ার নয়। সব রাস্তাই কি এখানে এসে মিশেছে?
গাড়িটা রাসেল স্ট্রিটের হবি সেন্টারের সামনে পার্ক করেছিলেন অশোক। রাত তখন সাড়ে বারোটা ছাড়িয়েছে, পায়ে হেঁটে চক্কর দেওয়া হয়ে গিয়েছে বেশ কয়েকবার। বন্ধুরা ঠিক করলেন, এবার বাড়ি ফেরা যাক।
পার্ক স্ট্রিটে তখন পশ্চিমমুখী গাড়ির ভিড় তুঙ্গে। মল্লিকবাজারের দিক থেকে শয়ে শয়ে ঘরমুখী গাড়ির চাপে ‘বাম্পার টু বাম্পার’ ট্রাফিক। বাপির কলকাতার রাস্তা চেনা হাতের তালুর মতো। বললেন, জওহরলাল নেহরু রোড ধরলে অনেক দেরি হয়ে যাবে সামান্য রাস্তা পেরতেই। তার চেয়ে রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড ধরে যাওয়া ভাল। ওয়েলিংটন হয়ে গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ-সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ পেরিয়ে স্ট্র্যান্ড রোড ধরে দক্ষিণে যাওয়াই সবচেয়ে কম সময়ের। ওদিকে তুলনায় এখন কম চাপ থাকবে গাড়ির।
বাপির দেখানো রাস্তায় এগোল লাল মারুতি। ওয়েলিংটনের কাছাকাছি আসতেই আরোহীদের চোখে পড়ল দৃশ্যটা। যা লিখেছি শুরুর অনুচ্ছেদে। একটা ট্যাক্সি ধাওয়া করেছে মোটরসাইকেলকে। যা চালাচ্ছেন একজন পুরুষ, পিছনে এক মহিলা। পিছু ছাড়ছে না ট্যাক্সি, গতি বাড়িয়ে-কমিয়ে চলেছে মোটরসাইকেলের গা ঘেঁষে। ট্যাক্সির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা হাত ছুঁতে চেষ্টা করছে মহিলাকে।
একটু এগিয়ে একসময় দ্বিচক্রযান থামিয়ে দিলেন চালক। মহিলাও নেমে দাঁড়ালেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ট্যাক্সি থামিয়ে নেমে এল পাঁচ যুবক। মোটরসাইকেল-চালকের সঙ্গে সামান্য কথাকাটাকাটির পর সরিয়ে দিল একরকম ধাক্কা দিয়েই। মহিলাকে ঘিরে ধরে শুরু হল কুৎসিত ইঙ্গিত, শরীরে অবাঞ্ছিত স্পর্শ।
‘অশোক,… এগিয়ে গিয়ে দাঁড় করা তো!’ পিছনের মারুতির সামনের সিট থেকে ঘটনাটা লক্ষ করছিলেন বাপি। কিছুটা এগিয়ে ব্রেক কষল গাড়ি। দরজা খুলে নেমেই ছুটলেন বাপি, ‘কী হচ্ছেটা কী? ছাড়ুন ওঁকে!’
—তুই কে শালা ফোঁপরদালালি করার? পাতলা হয়ে যা চটপট।
এসব হুমকিতে দমে যাওয়ার ছেলে ছিলেন না বাপি, একজনের হাত ধরে ফেললেন, ‘ছেড়ে দিন ওঁকে। আমার নাম বাপি সেন, টালিগঞ্জ ট্রাফিক গার্ডের সার্জেন্ট।’
উত্তর এল, ‘তো? আমরাও কলকাতা পুলিশের লোক। ফোট্!’
বাপি লড়ার চেষ্টা করেছিলেন সাধ্যমতো। পাঁচ যুবকের বেপরোয়া কিল-ঘুষি-লাথির তোড় অবশ্য সামলাতে পারলেন না বেশিক্ষণ। গৌতম-অশোক-কানাই-নাজিবুলরা ছুটে এলেন আটকাতে, পেরে উঠলেন না পালটা মারের ধাক্কায়। বাপি ততক্ষণে পড়ে গিয়েছেন ট্রামলাইনের উপর, তবু এলোপাথাড়ি লাথি অব্যাহত। সঙ্গে সমবেত চিৎকার, মেরে ফেল শালাকে।
গৌতম-সুব্রত-কানাই আবার এগোলেন আটকাতে, ‘কী করছেন কী? ও পুলিশ অফিসার।’
কে শোনে কার কথা? ‘শুনলি না, আমরাও পুলিশের! ও কি একাই পুলিশের নাকি? মেরে ফেল শালাকে!’
প্রতিরোধের চেষ্টা ব্যর্থ হল বন্ধুদের, রাস্তায় পড়ে থাকা বাপির শরীরে লাথির আঘাত পড়তে লাগল বেলাগাম। বুকে-পেটে-মাথায়-ঘাড়ে, কোথায় নয়?
বাপি যখন ট্রামলাইনের উপর নিস্পন্দ পড়ে নতুন বছরের প্রথম প্রহরে, ট্যাক্সিতে উঠে চম্পট দিল পাঁচজন। কানাই নোট করে নিয়েছিলেন ট্যাক্সির নম্বর, WB-04A-3450।
মোটরসাইকেলটা কোথায় গেল? ঝামেলা যখন তুঙ্গে, নিঃশব্দে চলে গিয়েছেন চালক ও সঙ্গিনী। সেটা কি গণ্ডগোলের সময় খেয়াল করেছিল আক্রমণকারী পাঁচজন? শিকার হাতছাড়া হওয়ার রাগেই কি ওই উন্মত্ত গণপিটুনি?
মোটরসাইকেলের খোঁজ নেওয়ার সময় নেই তখন। অচৈতন্য বাপিকে নিয়ে মারুতি ছুটল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। CB Top (ক্যাজ়ুয়ালটি ব্লক)-এর বেড নম্বর ১৫৮-য় ঠাঁই হল বাপির। রাত তখন দুটো বা তার আশপাশ। প্রাথমিক পরীক্ষার পর নাইটডিউটিতে থাকা চিকিৎসক বললেন, অবিলম্বে CT Scan করা দরকার। বন্ধুরা তখন দিশেহারা। কেউ বাপির বাড়িতে খবর দিচ্ছেন, কেউ ছুটছেন মেডিক্যালের কোথায় কীভাবে CT Scan হবে তার খোঁজে।
বউবাজার থানার সাব-ইনস্পেকটর রক্ষাকর মণ্ডল বেরিয়েছিলেন নাইট রাউন্ডে, রাত একটা নাগাদ। সাড়ে তিনটে নাগাদ মোবাইলে ধরল লালবাজার কন্ট্রোল, মেডিক্যাল কলেজে যান শিগগির, ওখানে বোধহয় একটা assault কেস আছে।’ ছুটলেন রক্ষাকর, মেডিক্যাল কলেজের পুলিশ আউটপোস্টের এএসআই ব্রজকিশোর চৌধুরির কাছে জানলেন বৃত্তান্ত। খবর পেয়ে টালিগঞ্জ ট্রাফিক গার্ডের তৎকালীন ওসি অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় রওনা দিলেন মেডিক্যালে, সঙ্গে বাপির মেজদা অনুপ।
CT Scan-এর রিপোর্ট দেখে ডাক্তার বললেন, আঘাত গুরুতর, অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পারেন। আলোচনার পর অনুপ সিদ্ধান্ত নিলেন, সিএমআরআই-তে নিয়ে যাবেন ভাইকে। জ্ঞান নিশ্চয়ই ফিরে আসবে দু’-একদিনের মধ্যে। দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি, জ্ঞান আর ফেরার নয়।
সিএমআরআই-এর আইসিইউ পরবর্তী ঠিকানা বাপির। নিউরোসার্জেন ডা. অজয় আগরওয়ালের নেতৃত্বে শুরু হল চিকিৎসা। ভোর হয়ে এসেছে তখন, কন্ট্রোল মারফত পুলিশমহলে জানাজানি হয়ে গিয়েছে ঘটনাপরম্পরা। ইভটিজিং রুখতে গিয়েছিলেন ট্রাফিকের সার্জেন্ট। পিটিয়ে আধমরা করে ফেলেছে পাঁচজন। যারা মেরেছে, তারাও শোনা যাচ্ছে পুলিশের লোক।
সকালেই ট্রাফিক কন্ট্রোলে দৌড়লেন রক্ষাকর। WB-04A-3450 নম্বরের ট্যাক্সির মালিকের নাম জানা গেল ডেটাবেস থেকে অল্পক্ষণের মধ্যেই। মধুকান্ত ঝা। ট্যাক্সির খোঁজও মিলল সহজেই। বিপিন বিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিটের পুলিশ মেসের সামনে, পাওয়া গেল মালিককেও। শুয়ে ছিলেন ট্যাক্সির মধ্যেই।
মধুকান্ত দ্বারভাঙার বাসিন্দা, চব্বিশ বছর আগে চলে আসেন কলকাতায়। পুলিশ মেসে রাঁধুনির কাজ দিয়ে শুরু। তারপর হিমালয় অপটিক্যালসে ড্রাইভারের কাজ দীর্ঘদিন। ’৯৬ -তে ধারদেনা করে নিজের ট্যাক্সি কেনেন। হেল্পার রেখেছিলেন দেশোয়ালি মেওয়ালাল গুপ্তাকে। পুলিশ মেসেই খাওয়াদাওয়া সারতেন দু’জন। চিনতেন মেসের পুলিশকর্মীদের প্রায় সবাইকেই।
কারা ট্যাক্সিতে ছিল গত রাতে? একটুও ভাবতে হল না মধুকান্তকে। এক কথায় বলে দিলেন পাঁচজনের নাম। মধুসূদন চক্রবর্তী, শ্রীদাম বাউরি, পীযূষ গোস্বামী ওরফে গোপাল, শেখরভূষণ গুপ্ত ওরফে ভোলা এবং শেখ মুজিবর রহমান। জানতে সময় লাগল না, পাঁচ কীর্তিমানই কলকাতা পুলিশের রিজার্ভ ফোর্সের কনস্টেবল। দিনের ডিউটির পর বর্ষশেষের রাতে বিনোদনে বেরিয়েছিলেন মধুকান্তের ট্যাক্সিতে সওয়ার হয়ে।
মধুসূদন আর পীযূষ গ্রেফতার হলেন মেস থেকেই। শ্রীদাম, মুজিবর আর শেখর ছিলেন না মেসে তখন। মধুসূদন আর পীযূষকে আদালতে পেশ করার সময় তদন্তকারী অফিসার রক্ষাকর আবিষ্কার করলেন, পালানোর পথ নেই বুঝে আদালতে আত্মসমর্পণের জন্য হাজির শ্রীদাম-মুজিবর-শেখর। পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হল পাঁচজনকে, সকলেই অস্বীকার করলেন অভিযোগ।
খবর প্রচারিত হল, চরম লজ্জায় পড়ল কলকাতা পুলিশ। রক্ষকই ভক্ষক, এহেন নৃশংসতায়? এক মহিলার মানইজ্জত বাঁচাতে মরিয়া লড়তে গিয়ে সতীর্থদের গণপ্রহারেই মৃত্যুশয্যায় পুলিশ অফিসার? মুখ লোকানো দায়, কলঙ্ক ঢাকার জায়গাই বা কোথায়?
বাপি তখন সংজ্ঞাহীন আইসিইউ-তে। ‘যমে-মানুষে টানাটানি’ লেখা গেল না। টানাটানি তখন হয় যখন উভয়েরই আংশিক জেতার সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে আগাগোড়া যমেরই নিরঙ্কুশ প্রাধান্য ছিল। বাপির শেষ নিশ্বাস ৬ জানুয়ারি, ভোর ৬টায়। খবর বেহালার বাড়িতে পৌঁছতে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন স্ত্রী সোমা, মা রেণুকা। গভীর শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল পর্ণশ্রী এলাকা। শুধু পর্ণশ্রী কেন, পুরো কলকাতাই ।
কলকাতা পুলিশের আংশিক কলঙ্কমোচনের একমাত্র উপায় ছিল দোষীদের দ্রুত শাস্তিবিধান। হোমিসাইড শাখার তৎকালীন ইনস্পেকটর অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্তমানে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার, দায়িত্ব নিলেন তদন্তের। পাখির চোখ, অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করা।
তদন্ত হোঁচট খেল শুরুতেই। বিস্তর চেষ্টাচরিত্র করেও খোঁজ পাওয়া গেল না নিগৃহীতা মহিলার, যাঁর বয়ান অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারত তদন্তের অগ্রগতিতে।
নগরপাল শেষমেশ খবরের কাগজে আবেদন জানালেন, ‘আপনি যে-ই হোন, আপনার মানসিক অবস্থা আমরা উপলব্ধি করতে পারছি। একান্ত অনুরোধ, অনুগ্রহ করে প্রকাশ্যে আসুন। আপনার হেনস্থা হওয়ার প্রতিবাদ করতে গিয়ে মারাত্মক জখম হয়েছিলেন আমাদের এক সহকর্মী বাপি সেন। আর বেঁচে নেই তিনি। দোষীদের শাস্তিদানে আপনার বয়ান খুবই জরুরি। আপনি সহযোগিতা করলে কৃতজ্ঞ থাকব। আপনার নিরাপত্তার সমস্ত দায়িত্ব কলকাতা পুলিশের।’
অপেক্ষাই সার, সাড়া মিলল না আবেদনে। তথ্যপ্রমাণ একত্রিত করে অতনুবাবু চার্জশিট পেশ করলেন ১০ মার্চ। শুরু হল বহুবিতর্কিত বিচারপর্ব।
অভিযুক্তদের আইনজীবী যুক্তি সাজালেন অনেক। তুলে দেওয়া যাক যুক্তিতক্কো আর গপ্পোর নির্যাস। এমন কোনও ঘটনা ঘটেইনি আদৌ। বাপি ওয়েলিংটনের কাছে ট্যাক্সি থামিয়ে নিজেকে সার্জেন্ট বলে পরিচয় দিয়ে লাইসেন্স আর ব্লু বুক দেখতে চান চালকের কাছে। বাপির মুখ থেকে মদের গন্ধ বেরচ্ছিল। চালক লাইসেন্স দেখাতে অস্বীকার করায় বাপি পিছনের দরজা খুলে উঠতে যান। ট্যাক্সি তখন চলতে শুরু করেছে। চলন্ত ট্যাক্সিতে উঠতে না পেরে রাস্তায় ট্রামলাইনের উপর পড়ে যান বাপি। দাবি, সেই আঘাতেই মৃত্যু। শ্লীলতাহানি-টানির কোনও গল্পই নেই।
ড্রাইভার মধুকান্ত এবং হেল্পার মেওয়ালাল, পুলিশি জেরায় যাদের বয়ান হুবহু মিলে গিয়েছিল বাপির বন্ধুদের বিবরণের সঙ্গে, বিরূপ সাক্ষ্য দিলেন আদালতে। সম্পূর্ণ উলটো কথা বলে বাপির মদ্যপ অবস্থায় পড়ে যাওয়ার তত্ত্ব সমর্থন করলেন।
সে-রাতে বাপি মদ্যপ ছিলেন, প্রমাণ করতে আদালতে পেশ করা হল মেডিক্যাল কলেজের আউটডোরের টিকিট। যাতে আঘাতের প্রাথমিক বর্ণনার পাশাপাশি লেখা ছিল, “two pegs of alcohol”। যার সূত্র ধরে প্রয়াত বাপির অসংযমী জীবনযাপনের সম্ভাব্য তত্ত্বও বিস্তারে আলোচিত হল আদালতে।
বলা হল, Test Identification Parade-এ বাপির বন্ধুরা যে অভিযুক্তদের সরাসরি শনাক্ত করেছিলেন, তা প্রমাণ হিসেবে মূল্যহীন। রাত সোয়া একটার সময় ঘটনাস্থলে এত আলো কোথায় যে মুখ চিনে রাখা যাবে? পুরোটাই গাঁজাখুরি গপ্পো, ফাঁসানো হচ্ছে অভিযুক্তদের।
দুর্ঘটনার কাল্পনিক তত্ত্ব খণ্ডন করতে সরকারি আইনজীবীর সহায় হল তদন্তকারী অফিসার অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠাসবুনোট চার্জশিট, যা তৈরি হয়েছিল যত্নশীল অধ্যবসায়ে।
ময়নাতদন্তে জানা গিয়েছিল, আঘাতের তীব্রতায় মাথার খুলিতে একাধিক চিড় ধরেছিল বাপির। শরীরের বাকি অংশে অগুনতি আঘাতচিহ্ন তো ছিলই। ডাক্তার স্পষ্ট লিখেছিলেন, মাথায় এবং শরীরের একাধিক আঘাতের কারণেই মৃত্যু, “ante-mortem and homicidal in nature.” দুর্ঘটনা নয়, খুনই।
অতনু জানতেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট নিয়ে বিচারপর্বে চাপানউতোর অনিবার্য। তাই রিপোর্টের বিষয়ে লিখিত মতামত নিয়েছিলেন ফরেনসিক মেডিসিনের দিকপাল বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডা. অজয় গুপ্তের। যিনি তখন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগের প্ৰধান।
অধ্যাপক গুপ্ত পোস্টমর্টেম রিপোর্ট খুঁটিয়ে দেখে সবিস্তার মতামত দিলেন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানালেন, আঘাত গাড়ি থেকে পড়ে হয়নি (nothing to suggest primary and secondary impact of a vehicle)। আরও লিখলেন, বচসা-হাতাহাতি দিয়েই সম্ভবত ঘটনার শুরু, কিছু ‘defensive wounds’ বা আত্মরক্ষাজনিত ক্ষতচিহ্নও ছিল বাপির শরীরে। কিন্তু মৃতের শরীরের যত্রতত্র অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন জানাচ্ছে, খুন করার উদ্দেশ্যেই লাথি-কিল-ঘুষি চলেছিল লাগামছাড়া। খুলিতে যে তীব্রতায় আঘাত লেগেছে একাধিক জায়গায়, সেটা শুধু ট্রামলাইনে পড়ে গিয়ে সম্ভব নয়। ভারী বুটজুতো জাতীয় কিছু দিয়ে মাথায় আঘাত করা হয়েছিল একবার নয়, বারবার।
উদ্ধৃত করি কয়েক লাইন, “Considering the site, size and disposition of injuries on the person of Bapi Sen, it could be concluded that the injuries resulted from fists, blows and kicks by healthy adult individuals with great force that was sufficiently strong to cause fracture of skull with intracranial and intracerebral injuries.”
বাপি কি সে-রাতে মদ্যপান করেছিলেন? আউটডোরের টিকিট যখন বাপির মৃত্যুর পর বাজেয়াপ্ত করেছিলেন অতনুবাবু, তাতে লেখা ছিল, “Beaten by fists, blunt injury, two pegs of alcohol.”
আশ্চর্যের, যিনি লিখেছিলেন, তাঁর কোনও সই ছিল না টিকিটে। আরও বিস্ময়ের, এক ঝলক দেখলেই বোঝা যায়, টিকিটে দু’রকম হাতের লেখা। আলাদা রঙের কালিতে। কোনও রকম রক্ত পরীক্ষা ছাড়াই কীভাবে লিখে দেওয়া হল নির্দিষ্টভাবে দু’ পেগের কথা? সে-রাতে বাপিকে নেশাগ্রস্ত প্রমাণ করতে তথ্যবিকৃতি ঘটানোর চেষ্টা হয়েছিল কোনও কোনও মহল থেকে, পরিষ্কার। ডক্টর আগরওয়াল তাঁর সাক্ষ্যে বলেছিলেন স্পষ্ট, পেশেন্টকে মেডিক্যাল কলেজ থেকে সিএমআরআই-তে আনার পর যখন প্রাথমিক পরীক্ষা করেছিলাম, আমার এতদিনের অভিজ্ঞতায় বলতে পারি, একবারও মনে হয়নি উনি ড্রিঙ্ক করেছিলেন।
আউটডোরের টিকিট এবং বাপির নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে যাওয়ার তত্ত্ব সোজা মাঠের বাইরে ফেলে দিয়েছিলেন নগর ও দায়রা আদালত। রায়ে আউটডোরের নথি প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, “Exhibit B has been manufactured…. because of the fact that at that relevant point of time the police officer those who are investigating the case were searching for other documents and evidence…”
আদালত স্বীকৃতি দিলেন Test Identification Parade-এর ফলকেও। ডিসি ডিডি লিখিত তথ্য চেয়েছিলেন Calcutta Electric Supply Corporation (CESC)-এর কাছে। সে-রাতে ঘটনাস্থলে কি বিদ্যুৎবিভ্রাট ঘটেছিল কোনও? যদি না-ও ঘটে থাকে, জায়গাটি কি যথেষ্ট আলোকিত ছিল? ঘটনাস্থলের কাছাকাছি থাকা আলোর বিবরণ দিয়ে জানিয়েছিলেন CESC-র চিফ ইঞ্জিনিয়ার, কোনও বিদ্যুৎবিভ্রাট ঘটেনি সে-রাতে। আলোকিত ছিল অকুস্থল, মুখ চিনে রাখার পক্ষে যথেষ্ট ছিল সে আলো।
যেখানে বাপির অকালমৃত্যু হয়েছিল
ছেঁদো যুক্তির কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতেছিল দুই প্রত্যক্ষদর্শীর বয়ান। গণেশ বারিক এবং সমীর ঘোষ। ৩৮/১, নির্মলচন্দ্র স্ট্রিটের ‘জয় মাতাদি ট্রেডার্স’ নামে এক বেসরকারি সংস্থার দুই নিরাপত্তারক্ষী। যাঁরা রাতপাহারায় ছিলেন এবং ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছিলেন।
বিচারক লিখলেন ১ জুলাই, ২০০৪-এর রায়ে, “এটি বিরলের মধ্যে বিরলতম কেসের পর্যায়ভুক্ত। শৃঙ্খলাবদ্ধ বাহিনীর সদস্য হয়েও দোষীরা যেভাবে নির্বিচারে গণপ্রহারে খুন করেছে বাহিনীরই আর এক অফিসারকে, তা অভাবনীয়। শুধুমাত্র দোষীদের বয়স বিবেচনা করে আমি প্রাণদণ্ড দেওয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখলাম, যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডিত হল দোষীরা।”
মামলা গেল হাইকোর্টে। নিম্ন আদালতের রায়কে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে সাজা বহাল রাখলেন উচ্চ আদালত। যাঁদের রায়ের প্রথম লাইনটি ছিল, “Once upon a time, there lived in the city of joy a soul who pledged his mortal frame to the battery of assault before a group of revelers when he had sought to prevent their onslaught on a damsel in distress, whom, they had zeroed on after trailing her two wheeler.” দুটি রায়েই লিপিবদ্ধ ছিল অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূয়সী প্রশংসা। নগরপালের প্রতি অনুরোধ ছিল নিখুঁত তদন্তের বিভাগীয় স্বীকৃতি দিতে।
সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করল অভিযুক্তরা। হাইকোর্টের রায়ে চোখ বুলিয়ে সর্বোচ্চ আদালত শুনানির প্রয়োজনই মনে করলেন না। সরাসরি নাকচ করে দিলেন আবেদন।
বাপির মা-বাবা প্রয়াত হয়েছেন। স্ত্রী সোমার চাকরির ব্যবস্থা করেছিল কলকাতা পুলিশ, বাপির মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই। বর্তমানে লালবাজারে ‘আর্মস অ্যাক্ট’ সেকশনে কর্মরতা। বড়ছেলে সোমশুভ্র এখন একুশ। কলেজের পাট চুকিয়ে চাকরির সন্ধানে। ছোট শঙ্খশুভ্র ক্লাস নাইন।
বাপি সেনের মৃত্যুর ইতিবৃত্ত যখন দিনের পর দিন দখল করে রেখেছিল খবরের কাগজগুলোর প্রথম পাতার সিংহভাগ, বিস্তর নিউজ়প্রিন্ট খরচ হয়েছিল আলোচনায়, কেন প্রকাশ্যে এলেন না নিগৃহীতা? যাঁকে বাঁচাতে গিয়ে অকালপ্রয়াণ পঁয়ত্রিশের তরতাজা অফিসারের, তিনি কেন নেপথ্যচারিণী হয়ে থাকলেন এটা জেনেও, তাঁর সাক্ষ্য অপরাধীদের শাস্তিপ্রাপ্তি নিশ্চিত এবং ত্বরান্বিত করবে? স্বয়ং নগরপালের আন্তরিক আবেদনেও কেন রহস্যাবৃতই রেখে দিলেন পরিচয়? ভোগেননি বিবেকের দংশনে, মনুষ্যত্বের তাড়নায়?
উত্তর অজানাই রয়ে গিয়েছে। তবে নির্বিচার দোষারোপের আগে যুবতীর দৃষ্টিকোণ থেকেও বিষয়টি বিচার্য বোধহয়। জানতেন, প্রকাশ্যে এলে পড়তে হবে পুলিশি জেরার মুখে, যা অবধারিত গড়াবে আদালতে সাক্ষ্যদান পর্বে। চাননি হয়তো ওই আইনি অণুবীক্ষণে নিজেকে মেলে ধরতে। আইন-আদালত-পুলিশ নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-আশঙ্কা তো থাকেই। জানতেন, গসিপ-বুভুক্ষু মিডিয়া ঝাঁপিয়ে পড়বেই ব্যক্তিজীবনের কাটাছেঁড়ায়, জেরবার হয়ে যাবেন ‘এক্সক্লুসিভ’ সাক্ষাৎকারের টানাহ্যাঁচড়ায়। পারেননি হয়তো সেই সম্ভাব্য সামাজিক চাপ সহ্য করার সাহস দেখাতে। সবাই পারেন না। বস্তুত, অধিকাংশই পারেন না। আর সেই ‘না-পারা’টার দায় সামাজিক প্রেক্ষিতকে উপেক্ষা করে পুরোটাই ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেওয়া কিঞ্চিৎ অন্যায্যই।
এবং এই একুশ শতকের প্রায় বছর কুড়ি কেটে যাওয়ার পরও যখন শ্লীলতাহানির ঘটনায় মধ্যযুগীয় প্রশ্ন ওঠে নিগৃহীতার বেশভূষা নিয়ে, কে বলতে পারে, নামধাম জানলে সামাজিক বিচারসভাই বসে যেত হয়তো কোনও কোনও মহলে, কাঠগড়ায় হয়তো দাঁড় করিয়ে দেওয়া হত যুবতীকেই, মধ্যরাতে পুরুষসঙ্গীর সঙ্গে নৈশভ্রমণের ‘অপরাধে’? সাহস দেখালে ভালই হত, স্বীকার করি। কিন্তু না দেখানোর মধ্যেও তেমন গর্হিত কিছু দেখি না।
বাপি সেনের হত্যা আজও দগদগে ক্ষতচিহ্ন হয়ে আছে কলকাতা পুলিশ পরিবারের মননে। রবিঠাকুর লিখেছিলেন, “সত্যরে লও সহজে”। উনি ক্রান্তদর্শী ছিলেন, ওঁর মতো কি আর ভাবতে পারি আমরা সাধারণরা, হাজার চেষ্টা করলেও?
সব সত্যি কি আত্মস্থ করা যায় অত সহজে? সহজে কি আর মেনে নেওয়া যায় এক সহকর্মীর এভাবে অকালমৃত্যু, এক অসহায় যুবতীর আব্রু রক্ষা করতে গিয়ে?
১.১১ দ্য বিলিয়ন ডলার কেস
[হোটেল পেঙ্গুইন হত্যামামলা
তদন্তকারী অফিসার শুভাশিস ভট্টাচার্য]
“নো স্যার! টেলিফোন ইয়েস, টেলিগ্রাফ ইয়েস, টেলিস্কোপ ইয়েস, টেলিপ্রিন্টার ইয়েস, বাট টেলিপ্যাথি?… নো স্যার!”
‘সোনার কেল্লা’-র দৃশ্য মগজে হানা দিয়ে যায় লেখা শুরু করতে গিয়ে। কপালজোরে প্রাণে বেঁচে যাওয়া ‘আসল’ ড. হাজরা, সারা মুখে ব্যান্ডেজ, সাহায্য চাইতে এসেছেন রাজস্থানের থানায় অপহৃত মুকুলের খোঁজে। কৌতুক আর অবিশ্বাসের মিশেল ইনস্পেকটরের চোখেমুখে। ড. হাজরা ‘প্যারাসাইকোলজিস্ট’ হিসেবে নিজের পরিচয় দিতে কিছুটা ঘাবড়েই গেলেন অফিসার, এ শব্দ কস্মিনকালে শোনেননি। ড. হাজরা তবু শেষ চেষ্টা করলেন মরিয়া, “আপ টেলিপ্যাথি জানতে হ্যায়?” এর পরই অফিসারের সেই “নো স্যার!…”
বিলিয়ন ডলার কোয়েশ্চেন ইয়েস, বিলিয়ন ডলার স্মাইল ইয়েস, বিলিয়ন ডলার ডিল ইয়েস, বাট বিলিয়ন ডলার নোট?
আমাকে-আপনাকে প্রশ্ন করলে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হবে ওই অবধারিত “নো স্যার!” যেমন হয়েছিল আমাদের হোমিসাইড বিভাগের গোয়েন্দাদের, আজ থেকে বছর পনেরো আগে বউবাজার থানার একটি খুনের মামলায়। কিনারা হওয়ার পর আদালতের বিচারপর্বে যে কেসের নামই হয়ে গিয়েছিল, ‘দ্য বিলিয়ন ডলার কেস।’
কেস নম্বর ৪৯, তারিখ ০৭.০২.২০০৩। থানা, আগেই লিখেছি, বউবাজার। খুনের মামলা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায়।
ধর্মতলা থেকে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ ধরে উত্তর দিকে হাঁটা দিলে ডান হাতে পড়ে যদুনাথ দে রোড। মধ্য এবং উত্তর কলকাতার বহু পুরনো রাস্তাগুলি যেমন হয়। চাকচিক্য নেই, আভিজাত্য আছে। নতুনের দেখনদারি নেই, পুরনো সেই দিনের কথা আছে। ‘হোটেল পেঙ্গুইন’ এই রাস্তা ধরে কিছুটা এগোলেই। এ অঞ্চলে যথেষ্ট নামডাক আছে এই হোটেলের। গুগল ম্যাপে ‘যদুনাথ দে রোড’ লিখে সার্চ দিলে দুটো কাছাকাছি দিকচিহ্ন পাবেন। একটা সেন্ট জোসেফস্ কলেজ, অন্যটা এই হোটেল পেঙ্গুইন।
৭ ফেব্রুয়ারি, ২০০৩। সকাল গড়িয়ে একটু বেলার দিকে ফোন বাজল বউবাজার থানায়, স্যার, হোটেল পেঙ্গুইন থেকে বলছি। তাড়াতাড়ি আসুন, মার্ডার! থানা থেকে গাড়িতে খুব বেশি হলে পাঁচ মিনিটের দূরত্ব, অফিসাররা ছুটলেন। খবর গেল ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টে। তড়িঘড়ি রওনা দিলেন হোমিসাইড শাখার গোয়েন্দারাও।
কী ব্যাপার? হোটেলের দু’তলায় রুম নম্বর ১০২, ডাবল-বেড। ৬ তারিখ সকালে দু’জন এসে ওই রুমে ওঠেন। রেজিস্টারে নাম রয়েছে, সুমন বিহারি আর মতিলাল সাউ। সন্ধের দিকে মতিলাল হোটেল থেকে বেরিয়ে যান। রাতে ফিরতে দেখেনি কেউ। পরের দিন সকালে হোটেলের হাউসকিপিং-এর কর্মীরা নিয়মমাফিক ঘরে ঘরে যাওয়া শুরু করলেন। শুধু ১০২ নম্বরের দরজা কিছুতেই খুলছে না, বারবার বেল বাজানো আর ‘নক’ করা সত্ত্বেও। কর্মীরা অপেক্ষাও করলেন কিছুক্ষণ। হয়তো বেশি রাত করে শুয়েছেন বোর্ডাররা, গভীর ঘুম ভাঙছে না সহজে। আধঘণ্টা পর আবার ডাকাডাকি, দরজায় শুধু টোকা নয়, এবার রীতিমতো ধাক্কা। তবু কোনও সাড়াশব্দ নেই। সন্দেহ এবং আশঙ্কা গাঢ় হল। ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে দরজা খোলার সিদ্ধান্ত নিলেন ম্যানেজার।
হোটেল পেঙ্গুইন
ঘরের ভিতরের দৃশ্য এইরকম। অবিন্যস্ত একটি বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ে আছেন সুমন বিহারি। নাড়ি টেপার দরকার নেই, এক ঝলক দেখলেই বোঝা যায়, প্রাণহীন শরীর। মৃতের শরীরে সাদা শার্ট, হাফ-হাতা ক্রিমরঙা সোয়েটার, ছাই রঙের ট্রাউজার। নাকমুখ দিয়ে চুঁইয়ে পড়া রক্ত জমাট বেঁধে আছে আশেপাশে। শরীরে আর কোথাও কোনও ক্ষতচিহ্ন নেই। লক্ষণ যা, সম্ভবত শ্বাসরোধ করে খুন। একটি খালি বিয়ারের বোতল ঘরের এক কোণে। আর ঘরের ডেস্কের উপর ৬ তারিখের ‘সংবাদ প্রতিদিন’ কাগজটি পড়ে। বারো পাতার কাগজের একটি পাতা নেই।
অনেকেই জানেন হয়তো, অপরাধের ঘটনাস্থলকে পুলিশি পরিভাষায় বলে P.O. (Place of Occurrence)। যে-কোনও অপরাধের তদন্তে P.O. হল সেই প্রথম সিঁড়ি, যার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণেই শেষ ধাপ পর্যন্ত পৌঁছনোর চাবিকাঠি লুকিয়ে থাকে কখনও কখনও। গোয়েন্দারা কিচ্ছু বাদ দিলেন না ঘরের। বিয়ারের বোতলটি খুঁটিয়ে দেখা হল। ‘ডেভেলপ’ করার মতো স্পষ্ট হাতের ছাপ নেই। তবু নেওয়া হল, যৎসামান্য যা পাওয়া গেল। ৬ তারিখের ‘সংবাদ প্রতিদিন’ কাগজটি সংবাদপত্রের অফিস থেকে আনা হল চটজলদি। যে পাতাটি ঘরে পাওয়া কাগজে ছিল না, সেটি দেখা হল মন দিয়ে। নাহ্, তদন্তে সাহায্য করার মতো কিছু নেই। ঘরে পাওয়া কাগজটির বাকি পাতাগুলিতেও কোথাও কিছু নেই হাতে লেখা, যা দিশা দেখাতে পারে।
রুম নং ১০২
বিছানার চাদর-বালিশ-তোশক, ডাস্টবিনের আনাচকানাচ, খাট-চেয়ার-টেবিল, আয়না-সিলিং ফ্যান-এসি, মায় বাথরুমের বেসিন-কমোড-সিস্টার্ন, ঘরের প্রতিটি সেন্টিমিটার-মিলিমিটার চিরুনিতল্লাশি করেও এমন কোনও সূত্র মিলল না, যা দিয়ে আততায়ীর কাছে পৌঁছনোর প্রাথমিক দিকনির্দেশ সম্ভব। মৃতের ট্রাউজ়ারের পকেট থেকে একটি নোটবুক ছাড়া, যাতে বেশ কিছু নাম-ঠিকানা, কিছু ফোন নম্বর। বেশ উৎসাহব্যঞ্জক ‘ক্লু’, ভাবলেন অফিসাররা।
নোটবুকের আদ্যোপান্ত দেখা হল। লিখে রাখা নাম-নম্বর যাচাই করে নিহত ব্যক্তির শনাক্তকরণ বিশেষ কষ্টসাধ্য হল না। মৃতের নাম সুমন বিহারি নয়। ভুল নামে উঠেছিলেন হোটেলে। আসল নাম তপন দাস, থাকতেন তপসিয়া থানার রাইচরণ পাল লেনে পেয়িং গেস্ট হিসেবে। পূর্ণচন্দ্র সাহা নামের এক মাঝবয়সির বাড়িতে। সাহাবাবু দেখা গেল নিপাট ভদ্রলোক, শনাক্ত করলেন মৃতকে। বললেন, তপন কম কথা বলতেন। মাঝে মাঝে কিছু লোকজন দেখা করতে আসতেন তাঁর সঙ্গে। তপন বলেছিলেন ব্যবসা করতেন, তবে ঠিক কীসের ব্যবসা, বিশেষ কিছু জানেন না সে ব্যাপারে। তবে তপন যে অবিবাহিত, এটুকু জানতেন। আত্মীয় বলতে নিহতের এক ভাইয়ের খোঁজ পাওয়া গেল খড়দহে। যিনি জানালেন, তপনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল না দীর্ঘদিন।
দাহ হওয়ার আগে ময়নাতদন্তে পাওয়া গেল প্রত্যাশিত তথ্য, খুন শ্বাসরোধ করেই।
‘হোটেলের ঘরে সঙ্গীকে খুন করে আততায়ী ফেরার, অন্ধকারে পুলিশ’ জাতীয় হেডিং দিয়ে খবর হল কাগজে। শহরে নাগরিক-নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা শুরু হল। আর অবধারিত চাপ তৈরি হল গোয়েন্দা বিভাগের উপর। কিনারা চাই, এবং দ্রুত। খুনিকে, সে যে-ই হোক, ধরে আনতে হবে।
লাও তো বটে, কিন্তু আনে কে! সত্যিই তখন অন্ধকারেই পুলিশ। হোটেলের কর্মীরা যাঁরা ছিলেন ৬ তারিখ ভোর থেকে পরের দিন ঘরের দরজা ভাঙা পর্যন্ত, কথা বলা হল সকলের সঙ্গে। কেমন দেখতে ছিল মৃতের সঙ্গীকে? উত্তরে যা পাওয়া গেল, তাতে এক ইঞ্চিও এগোল না তদন্ত। মাঝারি উচ্চতা, গায়ের রং সামান্য চাপা, চেহারা একটু মোটার দিকে। এটুকুতে হয়? এমন চেহারার শ’পাঁচেক লোক তো হোটেলের এক কিলোমিটারের মধ্যে পাওয়া যাবে অনায়াসে। চশমা ছিল? না। টাক ছিল? না। অন্য কোনও বিশেষত্ব চেহারায়, কোনও কাটা দাগ মুখে, বা খুঁড়িয়ে হাঁটার প্রবণতা? না স্যার, মনে পড়ছে না। কথা বলার কোনও বিশেষ ভঙ্গি? খেয়াল করিনি স্যার, হিন্দিতে কথা বলছিল রেজিস্টারে নাম লেখার সময়, তবে বাংলা টান ছিল।
মৃত যে বাঙালি, সে তো জানাই হয়ে গিয়েছে। ধরে নেওয়া গেল, সম্ভাব্য আততায়ী ‘মতিলাল’-ও বাঙালি। কিন্তু এই তথ্যের থেকেও ঢের বেশি জরুরি প্রশ্ন, ভুল নাম-ঠিকানা কেন রেজিস্টারে? নিজেদের হিন্দিভাষী বলে প্রমাণ করার চেষ্টা কেন? অপরাধের মতলব ছিল কোনও? থাকলে কী অপরাধ? সেখানেই কি লুকিয়ে রহস্যভেদের ঠিকানা?
মৃতের পকেট থেকে পাওয়া নোটবুকের প্রতিটি নাম-ঠিকানা, প্রতিটি নম্বরের ঠিকুজিকুষ্ঠি নিয়ে পড়লেন গোয়েন্দারা। প্রায় সব নম্বরই উত্তর চব্বিশ-পরগনার। বিস্তর তথ্যতালাশ করে জানা গেল, নানা ধরনের জালিয়াতিই ছিল মৃত তপনের পেশা বলুন বা জীবিকা। চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নাম করে বেকার যুবক-যুবতীদের টাকা আত্মসাৎ করা, তাড়াতাড়ি ব্যাংক থেকে লোন পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে লোক ঠকানো, আরও এই জাতীয়।
পাওয়া গেল আরও একটি তথ্য। সম্প্রতি এক অভিনব প্রতারণা-চক্রের পান্ডাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তপনের। অনেকের মনে থাকতে পারে, সেসময় ‘চাল টানা’-র গুজবে রীতিমতো হইচই পড়ে গিয়েছিল উত্তর চব্বিশ পরগনার গ্রামাঞ্চলের বিস্তীর্ণ অংশে। কাগজেও লেখা হয়েছিল বিষয়টি নিয়ে। ‘চাল টানা’ মানে? গুজব ছড়িয়েছিল, পুরনো দিনের হাঁড়িকুড়ি-বাসনপত্র নাকি চুম্বকের মতো টেনে নিচ্ছে কাছাকাছি থাকা চালের স্তূপকে। আর যে বাসনপত্র চাল টানছে, তা যে ধাতু দিয়ে তৈরি তার দাম নাকি আন্তর্জাতিক বাজারে আকাশছোঁয়া। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার স্বপ্নে একরকম প্রতিযোগিতাই শুরু হয়ে গেল বাড়িতে বাড়িতে। যে যার বাসনপত্র আর চাল জড়ো করে হা-পিত্যেশ করে ‘চাল টানা’-র অপেক্ষায়। তৈরি হল অশিক্ষা, গুজব আর লোভের ত্রিভুজ।
সুযোগটা লুফে নিয়েছিল কিছু প্রতারক। যারা ধাতু বিক্রির এজেন্ট হিসেবে পরিচয় দিয়ে ঘরে ঘরে ঢুঁ মারতে শুরু করল। এবং প্রতিশ্রুতি দিল, কিছু টাকা অগ্রিম দিলে তারা বাসনকোসনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ব্যবস্থা করে দেবে। অনেকে বিশ্বাস করে ঠকলেন। উল্লেখ্য, শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, দেশের অন্যান্য রাজ্যেও বিভিন্ন সময়ে এই ‘rice pulling trick’-এর নামে প্রতারণার ঘটনা ঘটেছিল।
উত্তর চব্বিশ পরগনায় ‘চাল টানা’-র সক্রিয় চক্রগুলির কয়েকটিকে পাকড়াও করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হল। কিন্তু লাভ হল না বিশেষ। শ্যামবর্ণ মাঝারি উচ্চতার মোটা লোকের কথা কেউ কেউ বলল বটে, কিন্তু ওটুকুই। নাম-ঠিকানার হদিশ মিলল না। যে তিমিরে ছিল, তদন্ত রয়ে গেল সেই তিমিরেই।
আপ্রাণ চেষ্টা করেও যখন সূত্র অধরা থাকে, তখন হতাশাগ্রস্ত না হয়ে পড়াটা দক্ষ তদন্তকারীর আবশ্যিক গুণের মধ্যে পড়ে। গোয়েন্দারা ঠিক করলেন, আবার শূন্য থেকে শুরু করবেন। ফিরে যাওয়া হল হোটেলে। শুরু হল আর এক প্রস্থ প্রশ্নোত্তর হোটেলকর্মীদের নিয়ে। ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অনন্ত ধৈর্য লাগে একই প্রশ্ন অনেককে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অসংখ্যবার করতে। তবু করে যেতেই হয়, কার কথায় কী কখন বেরিয়ে আসে তার অপেক্ষায়। বারবার তোতাপাখির মতো আউড়ে যেতে হয়, আর একটু ভেবে দেখুন, আর কিছু মনে পড়ছে?
সম্ভাব্য সূত্র বেরিয়েও এল এক কর্মীর কথায়। রুম সার্ভিসে কাজ করেন। জানালেন, ৬ তারিখ দুপুরে এক প্লেট চিকেন পকোড়া আর স্যালাডের অর্ডার এসেছিল ১০২ নং রুম থেকে। এ তথ্য আমরা হোটেলের নথি থেকে আগেই পেয়েছিলাম, অজানা ছিল না। প্রথম অর্ডারের কিছুক্ষণ পর রুম সার্ভিসে এসেছিল দ্বিতীয় অর্ডার, চিকেন পকোড়া আর এক প্লেট। এটাও জানাই ছিল। বাড়তি কিছু জানালেন কর্মীটি। বললেন, দ্বিতীয় বার যখন খাবার দিয়ে বেরিয়ে আসছেন, দুই বোর্ডারের মধ্যে তর্কাতর্কি হচ্ছিল। কী নিয়ে তর্ক? কর্মীটির যতদূর মনে পড়ছে, ‘সার্কাস’ শব্দটি শুনেছিলেন কয়েকবার।
‘সার্কাস’? এ-ই কি তা হলে সেই কাঙ্ক্ষিত সূত্র? এরা কি সার্কাসের সঙ্গে যুক্ত ছিল কোনও ভাবে? ঘটনার আগের দিন সার্কাস দেখেছিল? ঠকিয়েছিল কোনও সার্কাসের কর্মীকে?
আজকাল সার্কাসের সেই রমরমা নেই। যখনকার কথা লিখছি, তখন ছিল। শহরে তো বটেই, গ্রামেগঞ্জেও তুমুল জনপ্রিয় ছিল সার্কাস। খুনের ঘটনা ফেব্রুয়ারি মাসের, শীত তখনও ছুটি নেয়নি। সার্কাসের দলগুলিও তাঁবু গোটায়নি। হইহই করে বেরিয়ে পড়া হল, চষে ফেলা হল শহর ও আশেপাশের জেলার নামী-অনামী সার্কাস। সম্ভাব্য আততায়ীর ছবি (বিবরণ অনুযায়ী হাতে আঁকা) দেখিয়ে অনুসন্ধান হল যতরকম ভাবে সম্ভব। ফল কিন্তু শূন্য, আততায়ীর পরিচয়ের সামান্যতম ইঙ্গিতও পাওয়া গেল না।
এ বার? কূলকিনারা পাওয়ার আর রাস্তা কই? হতাশ তদন্তকারী দল ফিরছিল নৈহাটির একটি সার্কাসের খোঁজখবর নিয়ে, শূন্য হাতেই। কেসের কিনারা বোধহয় আর হল না, এই আক্ষেপকে সঙ্গী করে। কিন্তু ওই যে, “কখনও সময় আসে, জীবন মুচকি হাসে, ঠিক যেন পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনা…”। কলকাতা ফেরার পথেই কিনারাসূত্র এল আচম্বিতে, পড়ে পাওয়া চোদ্দো আনার মতোই।
গাড়ি ছুটছিল নৈহাটি পেরিয়ে জগদ্দলের দিকে, ঘোষপাড়া রোড ধরে। পরিশ্রান্ত অফিসারেরা ঠিক করলেন, কোথাও গাড়ি থামিয়ে একটু চা খাবেন। ড্রাইভারের বাড়ি নোয়াপাড়ায়। বললেন, সামনেই সার্কাস মোড়। ওখানে দাঁড় করাচ্ছি, ভাল দোকান আছে। গাড়ি দাঁড়াল জগদ্দলের সার্কাস মোড়ে। চা খেতে খেতে হঠাৎ আলোর ঝলকানি দেখলেন এক অফিসার। অন্যদের বললেন, আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, রুম সার্ভিসের ছেলেটা পুরোটা খেয়াল করেনি। সার্কাস মোড়ের ‘সার্কাস’-টুকু শুধু স্মৃতিতে থেকে গিয়েছে। আততায়ী যে প্রতারকদের সঙ্গে ওঠাবসা করেছিল, সবই তো উত্তর চব্বিশ পরগনার। সার্কাস মানে এই সার্কাস মোড় নয় তো? অন্যরা ভাবলেন, সত্যিই তো, কর্মীটি তো আর আড়ি পাততে ঘরে ঢোকেনি। অত খেয়াল করা বা মনে রাখার কথাও নয়। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর ‘সার্কাস’-ই হয়তো শুধু মনে করতে পেরেছে। খোঁজ নিয়ে দেখাই যাক না সার্কাস মোড়ের সংলগ্ন এলাকায়।
একাধিক অভিজ্ঞ সোর্স লাগানো হল জগদ্দলে, যারা সিঁধিয়ে গেল এলাকার অলিগলি-মহল্লায়। দিন দুয়েকের মধ্যেই খোঁজ মিলল একজনের, জগদ্দলেই বাড়ি। ‘মতিলাল’-এর চেহারার বর্ণনার সঙ্গে মিল প্রচুর, এলাকায় সুনাম নেই তেমন। আটক করা হল। আসল নাম জানা গেল, বাপি মুখার্জি। খুচরো চড়-থাপ্পড়ও দেওয়ার দরকার পড়েনি। লালবাজারের ‘ইন্টারোগেশন রুমে’ কড়া পুলিশি ধমকেই কাজ হল। এবং বাপির মুখ থেকে বেরোল সেই পাঁচটি শব্দ, যার থেকে বেশি শ্রুতিমধুর কিছু তদন্তকারী অফিসারদের কাছে হতে পারত না, ‘মারবেন না, সব বলছি স্যার!’
যে খুন হল এবং যে খুন করল, দু’জনেই ছিল ঝানু প্রতারক। বাপির সঙ্গে তপনের আলাপ হয় মাসখানেক আগে জগদ্দল স্টেশনে, চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, হওয়ারই ছিল। কিন্তু পরিণতি যে এত বিয়োগান্ত হতে যাচ্ছে, দু’জনেরই বোধহয় কল্পনার বাইরে ছিল। তপন একটা বিলিয়ন ডলারের জাল নোট পেয়েছিল তার কোনও প্রতারক বন্ধুর থেকে। এমন জাল মিলিয়ন-বিলিয়ন ডলারের নোট বিক্রি করার চেষ্টা করে ধরা পড়ার বেশ কিছু ঘটনা ইন্টারনেট ঘাঁটলেই পাবেন। অতীতে ঘটেছে দেশের বিভিন্ন প্ৰান্তে, ঘটেছে বিদেশেও। বাপির লোভ হয় দেখে। জানত না, এমন নোটের অস্তিত্ত্বই নেই। আবার তপনও ছিল এলেমদার জালিয়াত, ‘চাল-টানা’-র ঠগবাজির সঙ্গে বাপি জড়িত জানতে পেরে দুষ্টুবুদ্ধি খেলে যায় মাথায়। বাপিকে বলে, এই ব্যবসায় সে পুরনো খিলাড়ি। তার অনেক চেনাজানা এজেন্ট আছে, যারা দুর্মূল্য ধাতুর বেচাকেনার কারবার করে। বিলিয়ন ডলার নোটপ্রাপ্তি তো এই কারবার করেই। কিছু টাকা দিলে বাপির সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবে তাদের।
তপন বুনো ওল হলে বাপিও ছিল বাঘা তেঁতুল। বিশ্বাস অর্জনের জন্য কিছু টাকা দিয়েও দেয় তপনকে। তপনও প্রতিশ্রুতিমতো বাপিকে নিয়ে রওনা দেয় কলকাতায় এজেন্টের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবে বলে। সম্ভবত ভেবেছিল, ভুলভাল কিছু লোকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে আরও কিছু টাকা হাতিয়ে নেবে। বাপি অন্য ছক কষেছিল, হোটেলে রাত্রে তপন ঘুমিয়ে পড়লে বিলিয়ন ডলারের নোটটি হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দেওয়ার। দুই প্রতারক একে অপরকে ঠকানোর উদ্দেশ্যে এসে উঠল হোটেলে, নিজেদের আসল নাম গোপন করে।
ঘটনার দিন দুপুরে বিয়ার খেতে খেতেই বাগবিতণ্ডার সূত্রপাত। এজেন্টের সঙ্গে দেখা করিয়ে দেওয়ার জন্য আরও টাকা দাবি করে তপন। ক্ষিপ্ত বাপি উত্তরে আগে দেওয়া টাকা ফেরত চায়। স্পষ্ট বলে দেয়, তার মনে হচ্ছে, পুরোটাই ধাপ্পাবাজি। দরকার নেই তার বহুমূল্য ধাতু বেচে বিলিওনেয়ার হওয়ার। তর্কাতর্কি থেকে হাতাহাতি। তপনের বিলিয়ন ডলার নোট ছিনিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করে বাপি। ধস্তাধস্তি শুরু হয় প্রবল। একসময় মরিয়া বাপি গলা টিপে ধরে তপনের। মৃত্যু নিশ্চিত হওয়ার পর কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করে। ঠান্ডা মাথায় ঘরে চাবি দিয়ে বেরিয়ে যায় সূর্য ডোবার পর, পকেটে নোটটি নিয়ে। পালানোর আগে সকালে কেনা ‘সংবাদ প্রতিদিন’-এর একটি পাতা বার করে নিয়েছিল। তাতে মুড়ে রেখে দিয়েছিল চাবিটি, যা উদ্ধার হয় জগদ্দলের বাড়ি থেকেই।
নোটটির কী হল? কয়েকবার একে-ওকে বিক্রি করার ব্যর্থ চেষ্টার পর বাপি বুঝে যায়, কানাকড়িও মূল্য নেই ওই কাগজের টুকরোর। ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছিল হতাশায়।
কিনারা তো হল, কিন্তু শাস্তি? গ্রেফতার-পরবর্তী তদন্ত একদিনের ক্রিকেট নয়, টি-২০-র বিনোদনী জগঝম্প তো নয়-ই। এ হল ধ্রুপদী টেস্ট ক্রিকেট, যা চূড়ান্ত পরীক্ষা নেয় ক্রিকেটারের ধৈর্য-সংকল্প-মনোসংযোগ-অধ্যবসায়ের। রান আসছে না ওভারের পর ওভার, বোলার দাপট দেখাচ্ছে নিরঙ্কুশ, তবু দাঁত কামড়ে লোটাকম্বল নিয়ে বাইশ গজে পড়ে থাকা। উইকেট পড়ছে না কিছুতেই, নির্বিষ পিচে আয়েশি আধিপত্য কায়েম করছে ব্যাটসম্যান, তবু লেংথ-লাইন অভ্রান্ত রেখে বোলারের অপেক্ষা করা ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা অসতর্ক স্ট্রোকের জন্য। তদন্ত-ও তাই, হতাশার জায়গা নেই কোনও। লেগে থাকতে হবে, নয়তো বিচারের শেষে হাতে থাকবে শুধু পেনসিল। মিথ্যে হয়ে যাবে প্রাক্-গ্রেফতার পর্বের ঘাম ঝরানো।
হোমিসাইড বিভাগের সাব-ইনস্পেকটর শুভাশিস ভট্টাচার্য তদন্ত করেছিলেন। পদোন্নতির পর বর্তমানে ইনস্পেকটর হিসেবে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অ্যান্টি-চিটিং শাখায় কর্মরত। তুখোড় তদন্ত করেছিলেন।
‘সংবাদ প্রতিদিন’-এর বাকি পাতাগুলি এবং খোওয়া যাওয়া পাতাটি যে একই কাগজের, সেটা প্রমাণ করতে হয়েছিল ফরেনসিক পরীক্ষায় । অভিযুক্তের হাতের লেখার নমুনা সংগ্রহ করে তার সঙ্গে হোটেলের রেজিস্টারে থাকা লেখার তর্কাতীত সাদৃশ্য প্রমাণ করা হয়েছিল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। যে চাবি দিয়ে ঘরের তালা বন্ধ করে পালিয়েছিল খুনি, বাজেয়াপ্ত হওয়া চাবিটি যে সেটিই, প্রমাণ করতে হয়েছিল তা-ও। চার্জশিটের জাল কেটে বেরনোর পথ ছিল না। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয় অপরাধী, এখন সংশোধনাগারে।
মামলার নির্যাস? বিষে বিষে বিষক্ষয়!
১.১২ অতি পুরাতন ভৃত্য
(লুথরা হত্যামামলা
তদন্তকারী অফিসার আশিক আহমেদ)
হুইস্কি, রাম, ভদকা, ওয়াইন, ব্র্যান্ডি। পরিপাটি সাজানো সুদৃশ্য ড্রয়িং রুমের লিকার ক্যাবিনেটে। দেশি নয়, বহুমূল্য বিদেশি ব্র্যান্ডের সব। সাধারণ পানীয়পিপাসুর নাগালের বাইরে।
হইহুল্লোড়ের পার্টি শেষে যেমন চেহারা হয় উচ্চবিত্তের বসার ঘরের। সোফার কুশন অবিন্যস্ত। কাচের সেন্টার টেবলে প্লেট গোটাতিনেক, কাঁটাচামচ সমেত। একটায় চিকেন রেশমি কাবাব দু’ টুকরো। পনির পকোড়ার আধখাওয়া অংশ আর একটায়। শসা-পেঁয়াজ-টমেটোর কয়েক কুচি তিন নম্বর প্লেটে। ফেলে ছড়িয়ে খাওয়ার পর যেমন পড়ে থাকে অবশিষ্ট। হাত মোছার পর দাগ ধরে যাওয়া পেপার ন্যাপকিন পড়ে ইতিউতি। দুটো গ্লাসে সোনালি তরলের তলানি, হুইস্কি।
তিনটে রংবেরং মোমবাতি জ্বলছে টেবিলে। গড়পড়তা সাইজের নয়, পেল্লায়। ক্রিকেটের উইকেটের থেকে একটু ছোট। পুড়তে সময় লাগে বেশ কয়েক ঘণ্টা। নেভেনি এখনও, জ্বলছে।
এহ বাহ্য। বিশাল ফ্ল্যাটের তিনটে প্রশস্ত বেডরুমের একটার দৃশ্য আমোদপ্রমোদের চিহ্নহীন। একটা লেপে বুক অবধি মোড়ানো, মহিলা পড়ে আছেন মেঝেতে। প্রাণ নেই আর, ঝলকের দেখাতেই বোঝা যায় দিব্যি। ডাক্তার না হলেও চলে।
বয়স যে পঞ্চাশ ছাড়িয়ে একান্ন, বোঝাই যায় না। দেখলে মনে হবে, খুব বেশি হলে কত আর, মাঝচল্লিশ। বয়সানুপাতে মহিলার চেহারা নির্মেদ। শরীরচর্চার অভ্যেস ছিল?
নিজেকে বাঁচাতে পারেননি শেষ পর্যন্ত। কিন্তু আততায়ীর কাছে বিনা যুদ্ধে জমিও ছাড়েননি, স্পষ্ট। লড়েছিলেন আপ্রাণ, প্রমাণ ধরা রয়েছে ডান হাতের মুঠোর মধ্যে আটকে থাকা কয়েক গাছি চুলে। এ চুল খুনির, বুঝতে গোয়েন্দা হওয়ার প্রয়োজন নেই। গলায় শুধু ফাঁসের দাগ নয়। হুক জাতীয় কিছুর আঁচড়ও দেখা যাচ্ছে। নখের কোণে ময়লার ছোপ। নিশ্চিত, ওই ছোপও ঘাতককে প্রতিরোধকালীন। বাঁচতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন, জানান দিচ্ছে চোখ-মুখ-ঘাড়-গলায় আত্মরক্ষাজনিত আঘাতের আভাস।
শ্বাসরোধ করে খুন, নির্মম এবং পরিকল্পিত। কে এভাবে গলায় ফাঁস দিয়ে মেরে ফেলল? কে, না কারা?
একটা ল্যাডার দরকার।
হ্যাঁ, তা ছাড়া তো আর উপায়ও নেই। দাঁড়ান, দেখছি।
দুধের প্যাকেটগুলো পড়ে আছে ফ্ল্যাটের বাইরে, মাটিতে। রোজ বাস্কেট থাকে রাখার জন্য। আজ নেই। অযত্নে পিঠোপিঠি পড়ে আছে টাইমস অফ ইন্ডিয়া, আনন্দবাজার পত্রিকা আর ইকনমিক টাইমস। দুধ যিনি দেন রোজ, কাগজ যিনি বিলি করেন দৈনিক, বেল বাজিয়ে বাজিয়ে ধৈর্য হারিয়ে চলে গিয়েছেন। আরও কত বাড়ি যাওয়ার আছে। সময় কোথায় অপেক্ষার? অন্যদিন একবার বেল বাজালেই দরজা খুলে দেয় নিক্কু। দীর্ঘদিনের কর্মচারী এ বাড়ির। আজ খোলেনি।
ঝাঁকা নিয়ে সবজিওয়ালা অবশ্য অপেক্ষায়। এ বাড়ি তার চেনা। ‘বালিগঞ্জের ভাবি’ প্রতি সপ্তাহেই টেলিফোনে অর্ডার দেন টাটকা শাকসবজির। যদুবাবুর বাজারের ‘মাইতি ভেজিটেবলস’-এর কর্মীকে হুকুমমাফিক সবজি দিয়ে যেতে হয় ফি হপ্তায়। অপেক্ষায় আরও দু’জন। কাজের লোক রাধা আর ড্রাইভার আয়ুব। সকাল ন’টা বেজে গেল। এমন হয়নি কখনও, হওয়ার তো কথা নয়। মেমসাহেবের যদি ঘুম কোনও কারণে না-ও ভেঙে থাকে, নিক্কু তো অন্তত খুলবে। সে কী করছে?
উলটোদিকের ফ্ল্যাট থেকে চিন্তিত মুখে বেরিয়ে এলেন অশোক পোদ্দার। অসিতমোহন লুথরা ব্যবসার কাজে দক্ষিণ ভারত গিয়েছিলেন গত পরশু। ভাইজ্যাগ থেকে ফোনে স্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে গত সন্ধেতেও। আজ সকাল থেকে মোবাইলে ফোন করে যাচ্ছেন সহধর্মিণীকে। নো রিপ্লাই। ল্যান্ডলাইনও নিরুত্তর। উদ্বিগ্ন হয়ে ফোন করেছেন প্রতিবেশী মিস্টার পোদ্দারকে। —দেখুন না একটু, কী হল?
ঘড়ির কাঁটা তখন সোয়া ন’টা ছাড়িয়েছে। অশোকের ফোনেই আয়ুবের সঙ্গে কথা বললেন অসিত লুথরা।
—গাড়িগুলো গ্যারেজে আছে?
—আছে সাব।
‘গাড়িগুলো’ বলতে দুটো। একটা টয়োটা করোলা, অন্যটা হন্ডা সিটি। দরজা খুলছে না দেখে আধঘণ্টা আগেই একতলার গ্যারেজে ঢুঁ মেরে এসেছেন আয়ুব। এই ভেবে, মেমসাহেব নিজেই কোথাও বেরিয়েছেন হয়তো জরুরি কাজে। সাহেব-মেমসাহেব দু’জনেই তো ভাল ড্রাইভিং জানেন।
গাড়ি গ্যারেজেই? দুশ্চিন্তা আরও বাড়ল মিস্টার লুথরার।
—আয়ুব, এক্ষুনি পারভিন ম্যাডামের বাড়ি যাও। খোঁজ নাও ওখানে আছে কি না।
—জি সাব।
ডোভার রোডে বাড়ি তলোয়ার দম্পতির। সুদেশ আর পারভিন। দু’জনেই সদ্য পঞ্চাশ পেরিয়েছেন। সুদেশের ব্যবসা চামড়ার সামগ্রী রফতানির। স্ত্রী পারভিন বাড়িতেই জিম চালান বেশ কয়েকবছর ধরে। লুথরা পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠতা তলোয়ারদের। একে অন্যের বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত। পারভিনের জিমে সপ্তাহে তিনদিন ঘাম ঝরাতেন অসিতের স্ত্রী রবিন্দর কউর লুথরা।
না, তলোয়ারদের বাড়িতেও নেই। আয়ুবের সঙ্গেই সুদেশ-পারভিন ছুটে এলেন লুথরাদের ফ্ল্যাটে। ভিড় জমে গিয়েছে ততক্ষণে কেয়ারটেকার আর নিরাপত্তাকর্মীদের। বেরিয়ে এসেছেন অন্যান্য ফ্ল্যাটের আবাসিকরাও। কৌতূহল-উদ্বেগ-আশঙ্কা, গাঢ় হচ্ছে ক্রমশ।
জি প্লাস সেভেন বহুতল। আটতলায়, টপ ফ্লোরেই ফ্ল্যাট লুথরাদের। মূল দরজায় অটোমেটিক লক। পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গিয়েছে ছাদে। ছাদের মাঝামাঝি একটা বেশ উঁচু দেওয়াল। টপকে এদিক-ওদিক পারাপার অসম্ভব। দেওয়ালটা ছাদকে ভাগ করে দিয়েছে। পশ্চিম অংশটা লুথরাদের ব্যক্তিগত মালিকানায়। সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠে কেউ যে ওই অংশে ঢুকে পড়বে, জো নেই।
ঢুকতে হলে ফ্ল্যাটের ভিতরের সিঁড়ি দিয়ে ঢুকতে হবে। যা বসার ঘরের পাশ দিয়ে উঠে গিয়েছে ছাদে। ছাদে লুথরাদের দিকের অংশে একটা গেট থাকে তালাবন্ধ, ভিতর থেকে। ফ্ল্যাটের ভিতরের সিঁড়ির মুখে একটা দরজা, তার পাশে চাবি রাখা থাকে গেটের। সেটা নিয়ে কেউ ছাদে উঠে গেট খুলে দিলে তবেই দেওয়ালের ওপার থেকে লুথরাদের অংশে আসা সম্ভব।
ছাদটা ভারী সুন্দর, চোখের আরাম। এক দিকে সার্ভেন্টস্ কোয়ার্টার, যেখানে নিক্কু থাকে। কাচ দিয়ে ঘেরা একটা ঘর পাশেই। পোষা দুটো ল্যাব্রাডর, ‘ফ্যান্ডি’ আর ‘বিগল’-এর রাত্রিবাস ওই ঘরেই। ঘাসের এক চিলতে লন, ফুলের বাগান ছিমছাম। পাথরের স্তূপের মধ্য থেকে কৃত্রিম ঝরনা। জল উছলে পড়ছে অনর্গল। মন ভাল হয়ে যায় দেখলে, আরও একটু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।
তিনটে গেট আবাসনের। একটা গাড়ি এবং লোকজনের ঢোকার। একটা বেরনোর। তৃতীয়টা ইমার্জেন্সি গেট, বন্ধই থাকে সাধারণত। আবাসিকরা থাকেন দুটো ব্লকে। ‘এ’ আর ‘বি’। দুটো ব্লকই আটতলার। একতলায় পার্কিং-এর ব্যবস্থা। ‘এ’ ব্লকে প্রতি তলায় তিনটে করে ফ্ল্যাট। Unit-I, Unit –II আর Unit-III। ‘বি’ ব্লকে দু’তলায় একটা ফ্ল্যাট। বাকি ফ্লোরগুলোয় দুটো করে। নাম ওই ‘Unit’ দিয়েই। সব মিলিয়ে চৌত্রিশটা ফ্ল্যাট, দুটো ব্লক মিলিয়ে। লুথরারা থাকতেন ‘বি’-তে।
নিরাপত্তায় বিনিয়োগে কার্পণ্য করেননি আবাসিকরা। দায়িত্ব দিয়েছিলেন ‘ম্যাক সিকিউরিটি সার্ভিস’ নামের বেসরকারি নিরাপত্তাসংস্থাকে। গেটে এবং দুটো ব্লকের একতলার রিসেপশনে তিন শিফটে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারায় থাকতেন একজন সুপারভাইজার এবং তিনজন নিরাপত্তাকর্মী।
লিফট এবং সিঁড়ি, দুটো করে প্রতি ব্লকে। একটা লিফট ইমার্জেন্সির জন্য, বন্ধ থাকত। লিফটম্যান ছিল না। আবাসিকরা নিজেরাই লিফট অপারেট করতেন। রিসেপশনে বন্দোবস্ত ক্লোজ় সার্কিট ক্যামেরার। যার সংযোগ প্রতিটি ফ্ল্যাটের সঙ্গে ভিডিয়ো লিঙ্কেজের মাধ্যমে। অপরিচিত কেউ কোনও ফ্ল্যাটে যেতে চাইলে রিসেপশন থেকে ছবি পাঠানো হত সংশ্লিষ্ট ফ্ল্যাটে, জানানো হত ইন্টারকমে। সবুজ সংকেত পেলে তবেই ছাড়পত্র মিলত লিফট বা সিঁড়িতে ওঠার। রোজকার পরিচিত গৃহকর্মীদের ছাড় ছিল এই সুরক্ষাবলয় থেকে। আবাসিকদের পরিচিত আত্মীয়বন্ধুদেরও, নিয়মিত যাতায়াতে যাঁদের মুখচেনা হয়ে গিয়েছে।
ফ্ল্যাটে ঢুকতে হলে ছাদে উঠে দেওয়াল টপকানো ছাড়া উপায় নেই, ল্যাডার দরকার একটা। জোগাড় হল। ওই মই বেয়ে কোনওমতে দেওয়াল টপকালেন আয়ুব। চাবি রাখা ছিল যেখানে থাকার। ফ্ল্যাটের ভিতর দিয়ে ছাদে ওঠার সিঁড়ির পাশে। গেট খোলার পর বাকিরা ঢুকলেন। নিক্কু কই? নেই কোত্থাও।
পোষা কুকুর দুটো কাচের ঘরে। তালাবন্দি, অস্থির। দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে, চিৎকার করছে। কখনও ফ্যান্ডি আর বিগলসকে এভাবে আটকে থাকতে হয় না। প্রতিটা ঘরে দিনভর স্বচ্ছন্দ বিচরণ বাধাহীন। সোচ্চার প্রতিবাদ স্বাভাবিকই।
বসার ঘরে গ্লাস-প্লেট-পানীয় আর বেডরুমে রবিন্দর কউর লুথরার মৃতদেহ। বিবরণ দিয়েছি শুরুতে। বাড়তি যেটুকু বলার, লেপ সরিয়ে দেখা গেল, মৃতার শরীরে ফুলফুল নীলরঙা ম্যাক্সি। পায়ে মোজা। গলায় ফাঁসের দাগ ছাড়া অন্য কোনও শারীরিক হেনস্থা হয়নি।
বেডরুমের আলমারি-ড্রয়ার লন্ডভন্ড। মিসেস লুথরা হাতে হীরের আংটি পরে থাকতেন সবসময়। সেটা তো গেছেই, সঙ্গে ড্রয়ার আর আলমারিতে থাকা প্রচুর গয়নাগাটি। নগদ সাড়ে তিন লক্ষ টাকা, যা ছিল চামড়ার ব্যাগে। এবং প্রায় চারশো মার্কিন ডলার। মোদ্দা কথা, মূল্যবান যা ছিল, সব লোপাট।
পুলিশে ইনফর্ম করা দরকার ইমিডিয়েটলি, আতঙ্কের ঘোর কাটিয়ে প্রথম মুখ খুললেন অশোক পোদ্দার। সায় দিলেন সুদেশ তলোয়ার, জাস্ট আ মিনিট। লালবাজার কন্ট্রোলের নম্বর সেভ করা আছে আমার। পারভিনের কাছে নম্বর ছিল বালিগঞ্জ থানারও। ফোনের কনট্যাক্টস লিস্টে তিনিও চোখ বোলাচ্ছেন দ্রুত।
সোয়া দশটায় ফোন বাজল কলকাতা পুলিশের কন্ট্রোল রুমে। তারও মিনিটখানেক আগে বালিগঞ্জ থানায়।
—মার্ডার, শিগগিরি আসুন, অ্যাজ় আর্লি অ্যাজ় পসিবল। ওসি আছেন?
—মার্ডার? কোথায়?
ত্রিপুরা এনক্লেভ। ৫৯, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড। শহরের অন্যতম অভিজাত এলাকায় উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা আবাসন। পূর্বদিকে এগোলেই বালিগঞ্জ সায়েন্স কলেজ। পশ্চিমে হাঁটা দিলে সেন্ট লরেন্স হাইস্কুল আর বালিগঞ্জ মিলিটারি ক্যাম্প।
সিকিউরিটি এজেন্সির রমরমা ব্যবসা ছিল চুয়ান্ন বছরের অসিত লুথরার। GI Securities। পরিধি বিস্তৃত দেশের বিভিন্ন শহরে, এমনকী বিদেশেও।
মিসেস লুথরা
সুখী পরিবার। বড়ছেলে কবীরের বয়স পঁচিশ। দক্ষিণ ভারতের ব্যবসা দেখাশোনা করেন। ছোট অঙ্গদ, কুড়ির কোঠা পেরিয়েছেন সদ্য। পড়াশোনা করেন লন্ডনে। ব্যবসার কাজে মিস্টার লুথরাকে প্রায়ই ট্যুরে যেতে হয়। যেমন গিয়েছিলেন ১৩ ফেব্রুয়ারি। ফেরার কথা ছিল একুশে। ফিরতে হল ১৫ তারিখ দুপুরের ফ্লাইটে, নৃশংসভাবে স্ত্রীর খুন হওয়ার খবর পেয়ে।
ফ্ল্যাটে যার থাকার কথা ছিল এবং নেই, সেই নিক্কু যাদব বছর চব্বিশের যুবক। বিহারের বাঁকা জেলায় বাড়ি। গত সাত বছর ধরে এ বাড়িতে কাজ করছে। যখন স্রেফ ষোলো-সতেরোর কিশোর, তখন থেকে। রান্নাবান্না করে, পাশাপাশি বাজারহাট, টুকটাক ফাইফরমাশ খাটা।
আয়ুব আরও পুরনো, বয়স প্রায় ষাট। লুথরাদের গাড়ি চালায় তেরো বছর হল। মিতা এবং সরস্বতী দুই দিনরাতের কাজের লোক। দু’জনেই ছুটি নিয়েছেন গত ১১ তারিখ থেকে। সাময়িক কাজ চালাতে রাধা বলে এক মহিলাকে দিন সাতেকের জন্য রাখা হয়েছে। প্রতিবেশীদের প্রশ্নের উত্তরে যিনি জানালেন, গত রাতে সাড়ে আটটায় মেমসাহেব ছেড়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন আজ সকাল-সকাল চলে আসতে। যখন রাতে রাধা ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরিয়েছিলেন, ঘরে এক ভদ্রলোক ছিলেন। নিক্কু তো ছিলই।
খুন এই আবাসিক বহুতলেই
কে ভদ্রলোক?
প্রদীপ লাল। বয়স পঞ্চাশের কোঠায়, টিনের কনটেনার তৈরির জমাটি ব্যবসা। থাকেন কাছেই, রোল্যান্ড রোডে। প্রদীপ ও তাঁর স্ত্রী সুনীলার বহুদিনের সামাজিক সখ্য লুথরা-পরিবারের সঙ্গে। অসিত লুথরার সঙ্গে আড্ডা দিতে প্রদীপ এসেছিলেন গতকাল সন্ধে সোয়া সাতটায়। অসিত নেই দেখে ঘণ্টাদেড়েক গল্পগুজব করেছিলেন মিসেস লুথরার সঙ্গে। খুনের খবর পেয়ে ত্রিপুরা এনক্লেভে চলে এসেছেন সকাল সাড়ে দশটার মধ্যে। গতকাল সন্ধেবেলা এসেছিলেন, নিজেই বললেন প্রতিবেশীদের।
বেশ। কিন্তু নিক্কু কোথায়? ভ্যানিশ?
ত্রিপুরা এনক্লেভ। ৫৯, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড।
রবিন্দর কউর লুথরা হত্যা মামলা। বালিগঞ্জ থানা কেস নম্বর ১৭/২০০৭। তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি। ধারা ৩০২/৩৯৪ আইপিসি। খুন ও লুঠ।
বালিগঞ্জ থানার অফিসাররা পৌঁছলেন। একটু পরেই চলে এলেন হোমিসাইড শাখার অফিসাররা। কন্ট্রোল রুম মারফত খবর ছড়িয়ে গিয়েছে।
এলে কী হবে, ঢুকতে পারলে তো! কমপ্লেক্সের প্রধান ফটক বন্ধ, সামনে জড়ো হয়েছেন আবাসিকরা। পুলিশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চলছে। প্রায় লাগোয়া বহুতল ‘সপ্তপর্ণী’-র বাসিন্দারাও খবর পেয়ে নেমে এসেছেন। শুনতে হচ্ছে, যা পুলিশকে সচরাচর শুনতে হয় এমন কোনও ঘটনার পর স্পটে গেলে।
এখন আর এসে কী লাভ, যা হওয়ার তো হয়ে গিয়েছে। কী করে আততায়ী এসে খুন করে যায় এভাবে? পুলিশের টহলদারি ভ্যানকে তো চোখেই পড়ে না এ তল্লাটে। আজ আটতলায় হয়েছে, কাল পাঁচতলায় হবে। পরশু চারতলায়।
এসবে অভ্যস্ত আমরা। বুঝিয়েসুঝিয়ে কোনওমতে ঢোকা হল। বাড়তি ফোর্স পৌঁছল লালবাজার থেকে।
ফ্ল্যাটে আঙুলের ছাপ মিলল একাধিক। আলমারিতে, গ্লাসে, সোফার হাতলে, বেডরুমের আয়নায়, ড্রয়ারে। নগরপাল প্রত্যাশিতভাবেই তদন্তের ভার দিলেন গোয়েন্দা বিভাগের হোমিসাইড শাখাকে। দায়িত্ব পড়ল তৎকালীন সাব-ইনস্পেকটর আশিক আহমেদের উপর, যিনি বর্তমানে তপসিয়া থানার ওসি।
হইচই হওয়ার কথা খবর ছড়িয়ে পড়ার পর। হচ্ছিলও। মাত্র তো বছর এগারো আগের কথা। শুরু হয়ে গিয়েছে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার রমরমা। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে সার দিয়ে সংবাদমাধ্যমের গাড়ি। গোটাদুয়েক ওবি ভ্যানও। ‘ব্রেকিং নিউজ়’ টিভি খুললেই, ‘বহুতলে নৃশংস হত্যা, অন্ধকারে পুলিশ’ কিংবা ‘নাগরিক নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্নের মুখে লালবাজার’। এবং নানা মুনির নানা মত।
হোমিসাইড শাখা অবশ্য এসবে বিচলিত হওয়ার কারণ দেখছিল না কোনও। খুব খাটাখাটনি যাবে না কিনারায়। আগামীকাল বা পরশুর হেডলাইন চোখ বুজলেই দেখতে পাচ্ছিলেন আশিক, ‘চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কিনারা মহিলা খুনের, ধৃত গৃহভৃত্য।’
সমাধান তো স্রেফ সময়ের অপেক্ষা। সোজা মামলা, ‘open and shut case’। ওই নিক্কু বলে চাকরটা খুন করে গয়নাগাটি-টাকাপয়সা হাতিয়ে পালিয়েছে। মার্ডার ফর গেইন। কিন্তু পালিয়ে যাবে কোথায়, আর কতক্ষণই বা?
মোবাইল ফোন ভারতে এসে গিয়েছে ঘটনার বারো বছর আগে। মুঠোফোন তখন সবার হাতে। নিক্কুরও ছিল। পাওয়াও গিয়েছে নম্বর। যদি বন্ধও করে দেয়, শেষ টাওয়ার লোকেশন আর কল ডিটেলস নিয়ে খুঁজে বার করতে বড়জোর আটচল্লিশ ঘণ্টা। কপাল ভাল থাকলে তারও কম। কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে technical surveillance-এর। বাংলা কী হবে? প্রযুক্তি-প্রহরা?
আত্মতুষ্টির ঘোর কাটল লুথরাদের ফ্ল্যাটে বসে বেডরুমের স্কেচ ম্যাপ তৈরি করার সময়ই। ফোন বাজল ল্যান্ডলাইনে।
‘হ্যালো, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল থেকে বলছি। একজন বাইশ-তেইশের যুবককে এখানে ভরতি করা হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। ট্রাফিকের লোক দেখতে পেয়ে অ্যাডমিট করেছে। রোড অ্যাক্সিডেন্ট, হেড ইনজুরি আছে। মানিব্যাগে আই ডি কার্ড থেকে ফোন নম্বরটা পেলাম। ছবিও আছে। নাম নিক্কু যাদব। আপনাদের বাড়ির কেউ? আমরা পেশেন্টকে এসএসকেএম-এ ট্রান্সফার করছি, কন্ডিশন আনস্টেবল।’
এটা কী হল? নিক্কু দুর্ঘটনাগ্রস্ত! হিসেব মিলছে না তো! আরও বড় অঙ্ক আছে খুনের নেপথ্যে, যার পরিণতি নিক্কুর প্রাণনাশের চেষ্টা?
টিম ছুটল এসএসকেএম-এ। নিক্কু কথা বলার অবস্থায় নেই, অচৈতন্য। চোখের কোণে জমাট বাঁধা রক্ত। ডাক্তার বললেন, সাইকেল থেকে মুখ থুবড়ে পড়েছে ফুটপাথে। ছড়ে গিয়েছে চোখমুখ। শক্ত কিছুতে আঘাত লেগেছে মাথায়। পেশেন্টের CT Scan জরুরি অবিলম্বে। জ্ঞান ফেরা দরকার। মাথার আঘাত বেশি হলে নিউরোলজিতে রেফার করা হবে, বাড়াবাড়ি হলে আইসিইউ তো রয়েইছে।
তদন্তকারী দলের একজন বললেন, ‘জ্ঞান ফিরলে ওর সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার। একটু আর্জেন্ট। শুনেছেন তো, একটা ব্রুটাল মার্ডার হয়েছে বালিগঞ্জে। ওই বাড়িতে কাজ করত ছেলেটি। ওর স্টেটমেন্ট ভাইটাল।’
ডাক্তারবাবু এমন ভঙ্গিতে তাকালেন, যেন ভস্ম করে দেবেন। মুখে বললেন, ‘প্রাণ বাঁচানো বোধহয় আপাতত বেশি ভাইটাল। জ্ঞান ফিরুক, আই মিন, যদি আদৌ ফেরে। তারপর কথা বলবেন।’
কেসের সমাধান সহজেই হতে চলেছে, এমন ধারণা হলে একটা প্রাথমিক ঢিলেঢালা ভাব আসেই। যেটা নিমেষে কেটে গেল নিক্কুর দুর্ঘটনায়। দ্রুত স্থির হল তদন্তের ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতি। উঠে এল অনেক প্রশ্ন, সম্ভাব্য থিয়োরির জল্পনাকল্পনা।
এক, সিসিটিভি ফুটেজ আদ্যোপান্ত খতিয়ে দেখা দরকার। কে কে কখন ঢুকেছে, কখন বেরিয়েছে লুথরাদের ব্লক থেকে গত চব্বিশ ঘণ্টায়। কিন্তু মুশকিল, রিসেপশনের ক্যামেরার অবস্থানটাই এমন, কেউ রিসেপশনের কাছে এসে কোনও ফ্ল্যাটে যেতে চাইলে তবেই ছবি উঠবে। রোজকার পরিচিত কেউ, সে বাসিন্দাই হোন বা ফ্ল্যাটগুলির নিত্যদিনের কর্মচারী বা নিতান্ত অপরিচিত, পাশ দিয়ে চুপচাপ সরাসরি লিফটে উঠে গেলে ছবি ওঠার প্রশ্ন নেই। বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো।
অসিত লুথরার নিজের সিকিউরিটি এজেন্সির ব্যাবসা, এই গোড়ার গলদটা চোখে পড়েনি? যাক গে, ফুটেজ দেখতেই হবে খুঁটিয়ে। যা পাওয়া যায়।
দুই, সমস্ত নিরাপত্তারক্ষী ও কাজের লোকদের তালিকা তৈরি করতে হবে। আবাসনের দুটো ব্লকেরই। জানতে হবে তাদের ঠিকুজিকুষ্ঠি। কারওর কি অপরাধের গোপন পূর্বইতিহাস আছে? কারওর সঙ্গে কি কোনও কারণে শত্রুতা তৈরি হয়েছিল লুথরা দম্পতির? জানতে হবে। অসিত লুথরার পেশাগত দিকটাও দেখা দরকার, কোনও গুরুতর ব্যবসায়িক শত্রুতা ছিল কারও সঙ্গে?
তিন, আবাসিকরাও সন্দেহের বৃত্তে। দ্রুত গতির জীবনযাপনে বিশ্বাসী ছিলেন শ্রীমতী লুথরা। বস্তুত, আবাসনের অধিকাংশ পরিবারই। বিলাসবহুল গাড়ি, জিম-টেনিস-গলফ-ক্লাব-কিটি পার্টি।
খুনের দিনটাও মাথায় রাখতে হবে। ১৪ ফেব্রুয়ারি, ভ্যালেনটাইনস ডে। এখন তো বছরের তিনশো পঁয়ষট্টি দিনই কোনও না কোনও দিবস। বছরটা সাতশো তিরিশ দিনের হলেই ভাল হত, মনে হয় এক এক সময়। দ্বিগুণ ‘অমুক ডে’, ‘তমুক ডে’ উদযাপনের সুযোগ পাওয়া যেত!
তখন, এগারো বছর আগে, এত হরেকরকম দিবসের চল ছিল না। বিত্তশালী মহলে ভ্যালেনটাইনস ডে-র ধুমধাম অবশ্য তখনকার দিনেও শুরু হয়ে গিয়েছে। লুথরাদের ফ্ল্যাটে পার্টি হয়েছিল সে-রাতে। মিস্টার লুথরার অনুপস্থিতিতে কে বা কারা এসেছিলেন প্রেমদিবসের নৈশবাসরে? কতক্ষণ ছিলেন? আবাসিকদের কেউ? না কি কোনও বহিরাগত? দুটো গ্লাস ছিল টেবলে। মিসেস লুথরা ছাড়া তা হলে কি একজনই ছিলেন? কে?
চার, আবাসিকদের প্রত্যেকের, সমস্ত গৃহকর্মী ও নিরাপত্তারক্ষীর মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে কল ডিটেলস আর টাওয়ার লোকেশন নিতে হবে। একজনও যেন বাদ না যায়। কে ঘটনার সময় কোথায় ছিলেন, জানতে হবে সব, পুঙ্খানুপুঙ্খ। নিতে হবে প্রত্যেকের ফিঙ্গারপ্রিন্ট, মিলিয়ে দেখতে হবে ঘটনাস্থল থেকে সংগৃহীত নমুনার সঙ্গে।
পাঁচ, সবসময়ের দুই কাজের লোক সরস্বতী ও মিতাকে ডেকে পাঠাতে হবে। দু’জনেরই একই সময় ছুটিতে যাওয়ার দরকার পড়ল? আর রাধাও তো সবে কাজে ঢুকেছে দিন পনেরো হল। এমন তো কতই হয়, উদাহরণ আছে অসংখ্য, বিত্তশালী পরিবারে গৃহকর্মী হিসেবে যোগ দিয়ে সব ঘাঁতঘোঁত জেনে নিয়ে ডাকাতির ছক।
ছয়, এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ, নিক্কুর দুর্ঘটনা। যদি নিক্কুই খুনি হত, যেমন ভাবা হয়েছিল শুরুতে, অনায়াসে সরে পড়তে পারত। যদুবাবুর বাজারের কাছে যখন মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে দেখেন ট্রাফিক কনস্টেবল, সঙ্গে কোনও ব্যাগ-ট্যাগ ছিল না। টাকাপয়সা-গয়নাগাটি নিক্কুই নিয়ে থাকলে একটা কিছু তো দরকার সেগুলো ভরার জন্য। সিকিউরিটি গার্ড বলেছেন, নিক্কু পৌনে ছ’টা নাগাদ বেরিয়েছিল বড় চটের ব্যাগ নিয়ে। ব্যাগটা গেল কোথায়? নিক্কু কি এমন কিছু দেখে ফেলেছিল, দরকার ছিল পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দেওয়ার? প্রত্যক্ষদর্শী থাকাটা আততায়ীর পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারত?
না কি দুর্ঘটনাটা নিক্কুই সাজিয়েছে? সন্দেহভাজনের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রশ্নই নেই, সে যতই চিকিৎসাধীন থাক। ভুললে চলবে না, যেভাবে খুনটা হয়েছে, যদি জড়িত থাকে একাধিকও, পরিচিত কাউকে থাকতেই হবে ষড়যন্ত্রে। হতেও পারে, নিক্কুই আততায়ীর জন্য দরজা খুলে দিয়েছিল গভীর রাতে।
সাত, আততায়ীর জন্য, না আততায়ীদের জন্য? মিসেস লুথরা শারীরিকভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন। তাঁকে কাবু করা একজনের পক্ষে অত সহজ নয়। নিক্কুর সঙ্গে যোগসাজশে অন্য কেউ বা কারা খুনটা করল, এবং পাছে লুঠের বখরা দিতে হয় বা ব্ল্যাকমেলের শিকার হতে হয়, তাই সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হল নিক্কুকে? অথবা, লুঠপাট স্রেফ পুলিশকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে, আদৌ নয় “murder for gain”, অন্য কারণ আছে?
আট, লুথরাদের দাম্পত্য সম্পর্কে কি কোনও টানাপোড়েন ছিল? জানা জরুরি। প্রদীপ লালের ভূমিকাতেও প্রশ্ন। বলছেন, বন্ধু অসিতের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। নেই দেখে মিসেস লুথরার সঙ্গে দেড়ঘণ্টা গল্প করেছিলেন। মোবাইল ফোনের যুগে প্রদীপ জানতেন না, অসিত বাইরে আছেন? বিশ্বাসযোগ্য? আর যদি ধরেও নিই, খোঁজ নেননি সেভাবে, বন্ধুপত্নীর সঙ্গে সৌজন্যের হাই-হ্যালো বা চা-বিস্কুট-কোল্ডড্রিঙ্ক বড়জোর আধঘণ্টা-পঁয়তাল্লিশ মিনিটে মিটে যাওয়ার কথা। ঘণ্টাদেড়েকটা একটু বেশি ঠেকছে না?
ধোঁয়াশা অনেক, খটকা বিস্তর। কী কী জানা দরকার, কী কী করা দরকার, নোটবইয়ে তালিকা বানাচ্ছিলেন তদন্তকারী অফিসার আশিক। যত সহজ হবে ভেবেছিলেন, তেমন আর হল কই? পিঠে হাত রাখলেন ওসি হোমিসাইড, ‘কী রে, কী এত ভাবছিস?’
আশিক তাকালেন, ‘কমপ্লিকেটেড লাগছে স্যার।’
ঘটনার যা ঘনঘটা, বাস্তবের গোয়েন্দা তো বলবেনই, ২১, রজনী সেন রোডের বাসিন্দা হলেও নিশ্চিত বলে ফেলতেন, “গোলমাল লাগছে রে তোপসে!”
এসএসকেএম হাসপাতালে হত্যে দিয়ে পড়েছিলেন গোয়েন্দারা। নিক্কুর জ্ঞান ফিরল বিকেল নাগাদ। সৌভাগ্যের কথা, CT Scan-এর রিপোর্ট জানাল, মাথায় চোট আছে। তবে ইন্টারনাল হেমারেজ নেই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া হবে ব্যথা কমার ওষুধ দিয়ে।
—ডাক্তারবাবু, ওর কাছে কিছু জানতে চাওয়ার ছিল। কথাবার্তা বলা যাবে?
—আজই বলতে হবে? পেশেন্ট ট্রমায় আছে এখনও।
—যদি সম্ভব হয়…
—দেখবেন, যেন বাড়তি স্ট্রেস না হয়…
ফের ডাক্তারবাবুর সেই ভস্ম-করা চাউনি। এবার উপেক্ষা করলেন অফিসার। ডাক্তার তাঁর কাজ করবেন। পুলিশ পুলিশের। নিক্কুর বয়ানেই রহস্যভেদের জাদুকাঠি লুকিয়ে থাকতে পারে, ডাক্তার কী করে বুঝবেন?
লালবাজারে তখন যুদ্ধকালীন ব্যস্ততায় কাজ চলছে। গোটা পঞ্চাশেক মোবাইল নম্বরের CDR (Call details record) এবং TL (tower location) সংগ্রহ করার কাজে নেমে পড়েছে technical wing। রাধা, আয়ুব আর নিরাপত্তারক্ষীদের বেশ কয়েকজনকে আনা হয়েছে লালবাজারে। যদুবাবুর বাজারের সবজির দোকানের মালিক মদন মাইতিকেও। তলোয়ার দম্পতি, অশোক পোদ্দার আর প্রদীপ লালও এসে পড়বেন কিছুক্ষণের মধ্যে। আর কাকে কাকে আজই ডাকা প্রয়োজন, তার তালিকা তৈরি হচ্ছে। কেউ না কেউ হয় মিথ্যে বলছেন নয় সত্য গোপন করছেন। বয়ানে অসংগতি খুঁজে বার করতে হবে।
আয়ুব কেঁদেই চলেছেন। এক স্থানীয় সোর্স খবর দিয়েছে, মাইনে বাড়ানো নিয়ে নাকি লুথরাদের সঙ্গে কিছুদিন আগে মনকষাকষি হয়েছিল আয়ুবের। চেপে ধরতে আয়ুব কেঁদে ফেললেন, ‘মেমসাহেব আমাকে খুব ভালবাসতেন। আমি এত বড় পাপ করতে পারি না স্যার!’
নিক্কুকে যখন লালবাজারে আনা হল, ধুঁকছে। চোখেমুখে যন্ত্রণার ছাপ স্পষ্ট। দ্বিধায় পড়লেন অফিসাররা, একে বেশিক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করা ঠিক হবে? হাঁটতেই তো পারছে না ভাল করে। জলটল খাওয়ার পর নিক্কু যেটুকু বলল, তাতে ফের নাটকীয় মোড় নিল তদন্ত।
‘মিস্টার লাল গত রাতে ন’টা নাগাদ চলে গিয়েছিলেন। রাধা সাড়ে আটটার সময়। এক পুরুষ এবং এক মহিলা রাত এগারোটা নাগাদ আসেন। মেমসাহেব নিজেই দরজা খুলেছিলেন। মহিলা জিনস আর টপ পরে ছিলেন। ভদ্রলোক কুর্তা-পাজামা, দু’জনকে আগে কখনও দেখেছি বলে মনে করতে পারছি না।
মেমসাহেব খুব ভাল রান্না করতেন। চাইনিজ-কন্টিনেন্টাল-মোগলাই, সব রকম রান্না আমাকে শিখিয়েছিলেন। রাতের খাওয়ার পর আমাকে কিচেনেই থাকতে বলেছিলেন। গেস্ট আসার কথা আছে, বলেছিলেন সোয়া দশটা নাগাদ।
ওই দু’জন আসার পর আমাকে কাবাব, পকোড়া বানাতে বললেন। বানালাম, স্যালাডও তৈরি করলাম। মেমসাহেব আর ভদ্রলোক ড্রিঙ্ক করছিলেন। অন্য মহিলা শুধু জল চেয়ে খেয়েছিলেন। আমি ট্রে–আইসবক্স সব সাজিয়ে দিয়েছিলাম। ফ্ল্যাটে প্রায়ই বেশি রাত অবধি পার্টি হত, জাগতে হত আমায়। ভোর রাত অবধি পার্টি চলছিল গতকাল। আমি কিচেনে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।
চিৎকার-চেঁচামেচিতে ঘুম ভেঙে গেল। তখন ক’টা বাজে মনে নেই। আড়াইটে-তিনটে হবে। মেমসায়েবের সঙ্গে ওই মহিলার তর্ক হচ্ছিল। ভদ্রলোক থামাতে চেষ্টা করছিলেন। মহিলা রেগেমেগে বেরিয়ে গেলেন। কুর্তা-পাজামা পরা ভদ্রলোক থেকে গেলেন। তারপর আর ঘুম হয়নি।
মেমসাহেব আমাকে বলেছিলেন, ভোরভোর বেরিয়ে পুজোর ফুল আর কিছু ওষুধ আনতে। আমি সাড়ে পাঁচটা-পৌনে ছ’টার মধ্যে বেরিয়ে পড়েছিলাম সাইকেল নিয়ে।’
—তখনও ভদ্রলোক ছিলেন?
—হ্যাঁ, মেমসাহেব আর উনি বেডরুমে ছিলেন। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ছিল।
—তারপর?
—যখন যদুবাবুর বাজারের দিকে যাচ্ছি ফুল কিনতে, পিছন থেকে একটা বাইক এসে ধাক্কা দিল। মেরে বেরিয়ে গেল। ল্যাম্পপোস্টে মাথা ঠুকে গেল। ফুটপাথে পড়ে গেলাম। তারপর আর মনে নেই।’
গোয়েন্দারা ধন্দে পড়লেন। সকালের শিফটের নিরাপত্তারক্ষীর বয়ানের সঙ্গে নিক্কুর বেরনোর সময়টা মিলে যাচ্ছে। যিনি নিক্কুকে বেরতে দেখেছিলেন ব্যাগ হাতে। খুনটা কি তা হলে হয়েছে নিক্কু বেরিয়ে যাওয়ার পর? না কি তারও আগে, বন্ধ বেডরুমে? মহিলা কে, যিনি রেগেমেগে চলে গেলেন আড়াইটে-তিনটে নাগাদ? কুর্তা-পাজামা পরিহিতেরই বা কী পরিচয়?
—ভদ্রলোককে দেখলে চিনতে পারবি? মহিলাকে?
—নিশ্চয়ই স্যার। একবার দেখলেই পারব।
ছবি-আঁকিয়েকে ডাকা হল সঙ্গে সঙ্গে। বর্ণনা অনুযায়ী শুরু হয়ে গেল ‘Portrait Parle’ আঁকা। পুরুষ-মহিলা, দু’জনেরই। সমস্ত আবাসিকদের ও কর্মীদের দেখানো হবে সেই ছবি, স্থির হল।
সেই দুপুর থেকে টানা চলছে খোঁজখবর, একে-তাকে জিজ্ঞাসাবাদ। দুপুর-বিকেল-সন্ধে গড়িয়ে রাত তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা। ঠিক হল, আজ রাতের মতো ইতি টানা যাক জিজ্ঞাসাবাদে। Technical wing-এর বিশ্লেষণ থেকে কিছু নির্দিষ্ট দিশা আবাসিকদের গতিবিধি সম্পর্কে মিলতে বাধ্য কাল সকালের মধ্যে। সরস্বতী-মিতাকে খবর পাঠানো হয়েছে। কাল এসে পড়বে। অন্য আবাসিকদের বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ বাকি, কাল হবে।
আশিক ভাবছিলেন, যতটুকু দেখা হয়েছে সিসিটিভি ফুটেজ, কুর্তা-পাজামা এবং জিনস-টপ পরা মহিলার ছবি ধরা পড়েনি। তা হলে? অবশ্য সিসিটিভির যা পজিশন, ফাঁকি দিয়ে ঢোকা যায় সহজে। না কি ওই দু’জন ওই ব্লকেরই কোনও আবাসিকদের অতিথি, নিক্কু চিনত না? অনেক ফ্ল্যাটেই ভ্যালেনটাইনস ডে-র খানাপিনা-নাচাগানা হয়েছে সে-রাতে। অপরিচিত অতিথি এসেছিলেন অনেক। তাঁদের মধ্যেই কেউ?
রাত পৌনে বারোটা। তলোয়ার দম্পতি, অশোক পোদ্দার আর প্রদীপ লাল নিজেদের গাড়িতে বেরিয়ে গেলেন আর এক প্রস্থ জিজ্ঞাসাবাদের পর। রাধা-আয়ুব-নিক্কুর জন্য লালবাজারের ট্রান্সপোর্ট সেকশন থেকে গাড়ি ডাকা হল।
আশিক তখন মনে করিয়ে দিচ্ছেন, তিনজনেই যেন কাল দশটার সময় উপস্থিত থাকে ত্রিপুরা এনক্লেভে। কথা আরও বাকি আছে। গাড়িতে ওঠার সময় কাঁধে হাত রেখে নিক্কুকে বললেন, ওষুধগুলো খাবি ঠিক করে।
নিক্কু মাথা নাড়ে, এবং একই সঙ্গে মুখ থেকে ছিটকে বেরোয়, ‘উঃ!’
আশিক কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নেন, ‘কী হল রে?’
—চোট আছে স্যার। ও কিছু নয়।
গাড়িতে উঠতে যাওয়ার মুহূর্তে থামান আশিক।
—এক মিনিট দাঁড়া। কোথায় চোট?
—ঘাড়ের কাছে।
এই সেই মুহূর্ত, ক্লান্তি-শ্রান্তি-ক্ষুধা-তৃষ্ণা বন্ধক রেখে তদন্তকারীর স্নায়ু নিজের অজান্তেই অতিসক্রিয় হয়ে ওঠার।
—দেখা তো, কোথায় চোট?
—পুরনো চোট স্যার।
—পুরনো কি নতুন, আমরা বুঝব। জামাটা খোল।
জামা খোলায় প্রবল অনীহা নিক্কুর চোখমুখে। এতক্ষণের যন্ত্রণাপীড়িত মুখে হঠাৎই দ্বিধা আর উদ্বেগের আঁকিবুকি।
ট্রান্সপোর্ট বিভাগের গাড়ির আর স্টার্ট দেওয়া হল না। তিনজনকেই ফের নিয়ে যাওয়া হল ইন্টারোগেশন রুমে। শার্ট খোলার পর নিক্কুর ঘাড়ের কাছে দেখা গেল গভীর আঁচড়ের দাগ। নখ চেপে বসলে যেমন হয়। ডাক্তাররা স্বাভাবিকভাবেই নিক্কুর মাথার আঘাত নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন, হয় গুরুত্ব দেননি ওই আঁচড়কে, নয় নজর এড়িয়ে গিয়েছিল।
—এটা কী করে হল?
—পড়ে গিয়ে স্যার। ওই যে বাইক ধাক্কা মারল সকালে…
—তবে যে বললি, পুরনো চোট? পড়েছিস তো মুখ থুবড়ে। ঘাড়ের পিছনে লাগল কী করে?
নিক্কু ঘামতে শুরু করেছে তখন। আশিকের এক সহযোগী অফিসার তেড়ে যান নিক্কুর দিকে, ‘কী হয়েছিল বল? স্যার, দুটো ঠিকঠাক পড়লেই সব উগরে দেবে গড়গড় করে। দেব?’
নিরস্ত করেন আশিক, ‘আঃ, হেড ইনজুরি আছে ওর। ছাড়ো, এমনিতেই বলবে।’
এমনিতেই বলল। একটা মিথ্যে ধরা পড়ে গেলে পোড়খাওয়া অপরাধীরও রক্ষণ ভেঙে পড়া স্রেফ সময়ের অপেক্ষা, অভিজ্ঞতা আমাদের। নিক্কু তো তুলনায় নেহাতই আনাড়ি, কী করে ব্যতিক্রম হবে? বলতে শুরু করল, আর স্তম্ভিত গোয়েন্দারা শুনতে থাকলেন।
—বেশ কিছুদিন ধরে প্ল্যান করেছি স্যার। যা মাইনে পেতাম, ওতে কোনওমতে সংসার চলত। বিহারের বাড়িতে টাকা পাঠিয়ে নিজের হাতে আর কিছু থাকত না। ভাবতাম, এভাবেই কি চাকরগিরিতে জীবনটা কেটে যাবে? সাহেব বাড়িতে থাকলে সম্ভব হত না কিছু করার। মাঝেমাঝেই ব্যবসার কাজে বাইরে যেতেন সাহেব। তেমন একটা সুযোগ খুঁজছিলাম।
—বুঝলাম। কিন্তু খুনটা করলি কেন? চুরি করেও তো পালাতে পারতিস?
—কোথায় পালাতাম স্যার? আপনারা বাড়ি থেকে ধরে আনতেন। ছবি আর ঠিকানা তো সাহেবের কাছে ছিলই। আমার ইচ্ছে ছিল গ্রামে জমিজমা কিনে চাষবাসের। তাই এমন কিছু করতে হত যাতে টাকাটা হাতে আসে, আর ধরাও না পড়ি।
—হুঁ…
—গত কাল সন্ধেয় মিস্টার লাল এলেন, চলে গেলেন পৌনে ন’টা নাগাদ। রাধা তার আগেই চলে গিয়েছিল। আমি খেয়েদেয়ে শুতে গেলাম। মেমসাহেবও ডিনার করে শুয়ে পড়লেন। ফ্যান্ডি আর বিগলসকে রাত্রি সাড়ে এগারোটা নাগাদ ছাদের কাচের ঘরে বন্ধ করে দিলাম। ওদের গলার বেল্টটা নিজের কাছে রাখলাম।
—বলে যা।
—একটা নাগাদ ছাদের কোয়ার্টার থেকে নেমে ফ্ল্যাটে ঢুকলাম। মেমসায়েবের বেডরুমে নক
করলাম। উনি বেশ কিছুক্ষণ পরে ভিতর থেকে বললেন, ‘কে?’ বললাম, ‘নিক্কু। প্রচণ্ড শরীর খারাপ লাগছে। খুব মাথা ব্যথা করছে। একটা ওষুধ দেবেন?’ উনি দরজা খুলে দিলেন। ঝাঁপিয়ে পড়লাম ওঁর উপর। উনি প্রস্তুত ছিলেন না, হকচকিয়ে গেলেন। আমি ধাক্কা দিয়ে ওঁকে মেঝেতে ফেলে বেল্ট দিয়ে গলায় ফাঁস দিলাম। উনি জিম করতেন, খুব ফিট ছিলেন। ঘাড়ে-পিঠে আঁচড়ালেন। হাতে হিরের আংটি পরে থাকতেন, চোখে খুব জোরে ঘুষি মারলেন।
—চোখের ওই রক্ত জমে যাওয়াটা তা হলে ঘুষি থেকেই?
—স্যার।
—বলতে থাক।
—মেমসাহেব পারলেন না। শ্বাস বন্ধ হয়ে গেল একটু পরে। এরপর আলমারির চাবি খুলে টাকাপয়সা-গয়নাগাটি নিয়ে ড্রয়ারে থাকা একটা চামড়ার ব্যাগে ভরলাম। সেদিন ভ্যালেনটাইন না কী যেন ছিল। ইশক-মহব্বতের দিন। বেলুন টাঙানো হয়েছিল অনেক ফ্ল্যাটে। প্রায়ই পার্টি হত তো ফ্ল্যাটে। ভাবলাম, পার্টির মতো করে সাজাই বসার ঘরটা।
মেমসাহেব যখন পড়ে আছেন বেডরুমে, আমি কিচেনে ঢুকে রান্না শুরু করলাম। চিকেন কাবাব, পনির পকোড়া। ক্যাবিনেট থেকে বোতল বার করে দুটো গ্লাসে মদ ঢাললাম অল্প। মোমবাতি রান্নাঘরেই ছিল, জ্বালালাম। ন্যাপকিন-কাঁটাচামচ সাজিয়ে টেবিলে এমন ভাবে রাখলাম, যাতে মনে হয় অনেক রাত অবধি পার্টি চলেছিল। সে রাতে রাধা চলে যাওয়ার পর আর কেউ আসেনি ফ্ল্যাটে। সব বানিয়ে বলেছি।
—বেরলি তো ভোর পৌনে ছ’টায়?
—হ্যাঁ, তার আগে বেরলে সন্দেহ করত সিকিউরিটিরা। শীতকাল ছিল, মাথার উপর দিয়ে একটা মাফলার জড়ালাম। যাতে আঁচড়গুলো তেমন চোখে না পড়ে। চটের ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। বেরিয়ে STD booth থেকে বাবলুকে ফোন করলাম।
—কে বাবলু?
—বাবলু মন্ডল। বিহারে আমার জেলাতেই বাড়ি, পরিচিত। আলিপুরের অনন্ত অ্যাপার্টমেন্ট থাকে। নরেন্দ্র বাগলিয়া সাহেবের বাড়িতে রান্নার কাজ করে। ওর কাছে টাকাগয়না ভরতি ব্যাগটা রেখে এলাম কাগজে মুড়ে। বাবলু অসুস্থ ছিল কিছুদিন ধরে। ওকে ঘটনার কথা কিছু বলিনি। বলেছিলাম, পরে এসে ব্যাগটা নিয়ে যাব। ও সরল মনে বিশ্বাস করেছিল। চটের ব্যাগটা রাস্তায় ফেলে দিয়েছিলাম।
—চামড়ার ব্যাগটা বাবলুর কাছেই আছে?
—হ্যাঁ স্যার।
—এখনই যাব। তার আগে অ্যাক্সিডেন্টের গল্পটা বল।
—যদুবাবুর বাজারের কাছে ইচ্ছে করে সাইকেল নিয়ে ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা মেরেছিলাম। জানতাম, লাগবে। অজ্ঞান হয়ে যেতে পারি। চেয়েওছিলাম, অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকি দু’দিন। এত তাড়াতাড়ি ছাড়া পেয়ে যাব, ভাবিনি।
—যদি মরে যেতিস বেকায়দায় লেগে?
—ওটুকু ঝুঁকি নিতেই হত স্যার। পালিয়ে গেলে তো সবাই আমাকেই সন্দেহ করত।
নিক্কু দম নেয় একটানে এতটা বলে। আশিক মোবাইলে ধরেন ডিসি ডিডিকে।
—স্যার, কেস ক্র্যাকড। নিক্কু কনফেস করছে। He only created the party scene.
রাতেই লালবাজার রওনা দিলেন গোয়েন্দাপ্রধান। এবং যখন মুখোমুখি হলেন নিক্কুর, আশিক বলে ফেললেন, ‘কঠিন জিনিস স্যার। শুনুন একবার গল্পটা। অস্কার না হোক, ফিল্মফেয়ারের বেস্ট অ্যাক্টর অ্যাওয়ার্ড এর বাঁধা।’
পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ এগোল প্রত্যাশিত পথে। সে-রাতেই অনন্ত অ্যাপার্টমেন্টে বাবলুর কোয়ার্টারে হানা দিল পুলিশ। বাবলুর কাছ থেকে পাওয়া গেল চামড়ার ব্যাগ। উদ্ধার হল সমস্ত টাকা-ডলার-গয়নাগাটি। যে বেল্টের ফাঁস দিয়ে খুন করেছিল রবিন্দর লুথরাকে, সেটা নিক্কু লুকিয়ে রেখেছিল ছাদের ঝরনার পাথরের চাঁইয়ের নীচে। পাওয়া গেল। পোস্টমর্টেম আর ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের মতামত জানাল, মৃতার গলায় আঁচড়ের দাগ বেল্টের হুক থেকেই হয়েছিল খুব সম্ভব। আর আঙুলের ছাপ তো ছিলই একাধিক জায়গায়। যা হুবহু মিলে গিয়েছিল নিক্কুর সঙ্গে।
খুনের প্রত্যক্ষদর্শী অমিল। কিন্তু পারিপার্শ্বিক প্রমাণ ছিল এতটাই সংশয়াতীত, চার্জশিট-উত্তর বিচারপর্বে আলিপুর জেলা ও দায়রা আদালত নিক্কু যাদবকে দোষী সাব্যস্ত করে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।
হাইকোর্টে আবেদন হল যথানিয়মে। সাজা কমে দাঁড়াল যাবজ্জীবন কারাবাসে।
ঘটনা ফিরে দেখলে মনে হয়, বিশ্বাস এক আশ্চর্য অনুভূতি। যখন সত্যিই করে কেউ, চেনা-পরিচয়ের সড়কপথে বেশ কিছুটা দূরত্ব অতিক্রমের পর, তা হয় শর্তহীন। ঠিক যেমন নিক্কুকে করেছিলেন মিসেস লুথরা। স্নেহ করতেন নিখাদ, বিশ্বাসও প্রশ্নহীন। টাকাপয়সা-গয়নাগাটি আলমারিতে খোলা রেখে বেরতেন নিশ্চিন্তে, নিক্কুর ভরসায়।
দূরতম কষ্টকল্পনাতেও ভাবেননি, বিশ্বাসভঙ্গ হবে প্রাণের বিনিময়ে। আর, কে ঘটাবে বিশ্বাসের অপমৃত্যু?
অতি পুরাতন ভৃত্য!
২. গোয়েন্দাপীঠ লালবাজার – ২য় খণ্ড
মুখবন্ধ
প্রথম দুটি বই বেস্টসেলার হওয়ার পর নিজের তৃতীয় বইটি লেখার সময় সুপ্রতিম কতটা চাপে ছিল সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই, তবে এই বইটির মুখবন্ধে কী লেখা উচিত সেটা ভাবতে গিয়ে যেন হঠাৎই বেশি সচেতন হয়ে পড়েছি। যদিও খুব বেশিসংখ্যক মনোযোগী পাঠক মুখবন্ধ পড়েন না বলেই আমার দৃঢ় ধারণা, তবু, কোন মুখবন্ধ-লেখকই বা চান হংসমধ্যে বকযথা হয়ে থাকতে? তা ছাড়া, যে বইয়ের প্রভাব যতটা বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তার মুখবন্ধটি পাঠকের চোখে পড়ার সম্ভাবনাও থাকে তুলনামূলক ভাবে বেশি। সে কারণেই এই লেখাটি লিখতে বসে বাড়তি সচেতনতা, সংগত উদ্বেগ।
সুপ্রতিমের লিখনশৈলী অবশ্য এতটাই সহজাত, আগের দুটি বইয়ের সাফল্য এবং পরবর্তীর প্রত্যাশা পূরণের কোনও চাপ এই বইটির লেখাগুলোয় চোখে পড়েনি আমার।
‘গোয়েন্দাপীঠ লালবাজার’-এর প্রথম খণ্ডের সার্থক উত্তরসূরি এই দ্বিতীয়টি, যাতে ধরা আছে কলকাতা পুলিশের মহাফেজখানা থেকে বেছে নেওয়া এগারোটি চাঞ্চল্যকর মামলার রহস্যকথা। প্রথম খণ্ডের তুলনায় এবারের কাহিনিগুলি তুলনায় বেশি সাম্প্রতিক। পাঠক নিশ্চিত লক্ষ করবেন, এই খণ্ডে স্থান পাওয়া মামলাগুলির তদন্তপ্রক্রিয়ায় কীভাবে ধরা পড়েছে বদলে-যাওয়া সময়ের ছাপ, ধরা পড়েছে প্রযুক্তির প্রভাব।
প্রযুক্তির প্রসার আজকের দুনিয়ায় একদিকে যেমন প্ররোচনা দেয় দুঃসাহসিক অপরাধে, আবার রহস্যভেদে তদন্তকারীর হাতিয়ারও হয়ে ওঠে সেই প্রযুক্তিই, যার সৌজন্যে ন্যায়বিচারের পথটিও প্রশস্ত হয়। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি তদন্তপ্রক্রিয়ায় কতটা নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারে, তার সেরা উদাহরণ রয়েছে হাতের সামনেই। এ বছরেই ঘটে যাওয়া একটি নৃশংস খুন, যা সাড়া ফেলে দিয়েছিল গোটা বিশ্বে। খুনটি একটি গোয়েন্দা সংস্থা করিয়েছিল বলে অভিযোগ উঠেছিল।
সৌদি আরবের সাংবাদিক জামাল খাসোগির হত্যার কথা বলছি, যিনি নিয়মিত লিখতেন ‘ওয়াশিংটন পোস্ট’ পত্রিকায়। খাসোগিকে শেষবার জীবিত দেখা গিয়েছিল তুরস্কে, সৌদি আরবের দূতাবাসে ঢোকার সময়। বাইরে অপেক্ষা করছিলেন তাঁর প্রেমিকা হ্যাটিস সেনগিজ। তুরস্কের নাগরিক হ্যাটিসের কাছে গচ্ছিত ছিল খাসোগির আই ফোন এবং অন্যান্য জিনিসপত্র।
খাসোগি সৌদি দূতাবাস থেকে আর বেরিয়ে আসেননি। সৌদি আধিকারিকরা দাবি করেছিলেন, খাসোগি অন্য কোনও গেট দিয়ে দূতাবাসের বাইরে বেরিয়ে গিয়েছেন।
খাসোগির মতো দেখতে একজন ইস্তাম্বুলের রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এমন সিসি টিভি ফুটেজও ঘটনার কয়েকদিন পর বাজারে ছেড়েছিলেন সৌদি অফিসাররা, কিন্তু তাতে এতটুকু চিঁড়ে ভেজেনি। সারা দুনিয়া অচিরেই জেনে গিয়েছিল খাসোগি-হত্যার চিত্রনাট্য। ঘটনার একদিন আগে রিয়াধ থেকে একটি বিশেষ বিমানে সৌদি সরকারের ‘সিক্রেট সার্ভিস’-এর পনেরো সদস্যের একটি দল যে তুরস্কে এসেছিল, এবং খাসোগির দেহ টুকরো টুকরো করে কেটে দেহাংশ পুড়িয়ে ফেলেছিল অ্যাসিড দিয়ে, সবই প্রকাশ্যে এসেছিল।
সত্যিটা প্রকাশ্যে আসত না প্রযুক্তি সহায় না হলে, চাপা পড়ে যেত সৌদি আরব আর তুরস্কের পারস্পরিক চাপান-উতোরে। খাসোগির অন্তর্ধানের রহস্যভেদ করেছিল তাঁরই ঘড়ি, তাঁরই ফোন। ‘অ্যাপল’-এর ঘড়ি পরতেন খাসোগি। ব্যবহার করতেন আই ফোন। দূতাবাসে ঢোকার আগে খাসোগি ঘড়ির সঙ্গে নিজের ফোনকে ‘কানেক্ট’ করে নেন, প্রযুক্তি-সংযোগে যা এক সেকেন্ডের ব্যাপার। তারপর হাতের ঘড়িকে ‘রেকর্ডিং মোড’-এ রেখে ঢোকেন দূতাবাসের ভিতরে। ফোন রেখে যান বাইরে অপেক্ষমাণ প্রেমিকার কাছে। যিনি ফোনটি তুরস্কের আধিকারিকদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন খাসোগি নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার দিনকয়েক পরে।
বলা বাহুল্য, খাসোগির সঙ্গে দূতাবাসের ভিতরে যা যা ঘটছিল, যা যা কথোপকথন হচ্ছিল, সবই রেকর্ড হয়ে যাচ্ছিল ফোনেও। খাসোগির মৃত্যুর বেশ কিছুক্ষণ পরও সক্রিয় ছিল ঘড়িটি। খাসোগির জামাকাপড় সহ ঘড়িটিও অ্যাসিডে পুড়িয়ে ফেলার পরই তা নিষ্ক্রিয় হয়। খাসোগি-হত্যার অকাট্য প্রমাণ যখন প্রকাশ্যে আসে ফোনের রেকর্ডিং-এর মাধ্যমে, সৌদি আরব হত্যার দায় স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এবং দাবি করে, খাসোগিকে খুনের সিদ্ধান্ত ‘জুনিয়র লেভেল’-এর আধিকারিকরা নিয়েছিলেন।
কল্পনার ক্রাইম থ্রিলারে ব্যর্থতার স্থান নেই। সব মামলারই সমাধান হয়ে যায় সেখানে। বাস্তব আলাদা। সেখানে সাফল্যের গা ঘেঁষেই থাকে ব্যর্থতাও। এই বইয়ে আমাদের ব্যর্থতার কাহিনিও ঠাঁই পেয়েছে। সুপ্রতিম এই খণ্ডে ‘স্টোনম্যান’ মামলার কথা লেখায় খুশি হয়েছি। এই সূত্রেই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই আর একটি ‘সিরিয়াল-কিলিং’ মামলার প্রতি, যা ঘটেছিল ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রানসিসকো বে-তে।
আজ থেকে ঠিক পঞ্চাশ বছর আগের ঘটনা। ১৯৬৮ সালের ২০ ডিসেম্বর দু’জন স্কুলপড়ুয়া ছাত্রছাত্রী গুলিতে খুন হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লেক হেরম্যান রোডে। এরপর কিছুদিনের মধ্যে আরও অন্তত তিনটি খুন হয় একই কায়দায়। সিরিয়াল-হত্যার এই মামলাগুলির নেপথ্যঘাতককে ‘Zodiac Killer’ নাম দিয়েছিলেন তদন্তকারীরা। তামাম আমেরিকায় সাড়া ফেলে দিয়েছিল খুনগুলি। ‘Zodiac Killer’-কে নিয়ে বহু বই লেখা হয়েছে। সাধারণ মানুষের কৌতূহলকে উস্কে দিতে তৈরি হয়েছে হলিউড ছবি, টিভি সিরিজ।
‘Zodiac’ সাংকেতিক ভাষায় পুলিশকে এবং সংবাদপত্রে চিঠিও পাঠাত। প্রথম চিঠিটির অর্থ বোঝা গেলেও দ্বিতীয়টির মর্মার্থ উদ্ধার করা যায়নি।
পুলিশ একটা পর্যায়ের পর মামলার তদন্ত থামিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু কিছু নতুন তথ্য পাওয়ার পর, তদন্তপদ্ধতির প্রযুক্তিগত প্রসারের পর, মামলাটির তদন্ত নতুন করে শুরু হয় ২০০৪ সালে। ‘Zodiac’-এর আসল পরিচয় অবশ্য এখনও অজ্ঞাত, এখনও তদন্তকারীরা চেষ্টা চালিয়ে যান সংকেত-সমাধানের। একটি চিঠিতে ‘Zodiac’ তার নিজের নামও সাংকেতিক ভাষায় জানিয়েছিল বলে দাবি করেছিল। পাঠকের হাতে তুলে দিলাম সেই বহুচর্চিত ‘কোড’, যার রহস্যভেদ আজও অধরা।
কলকাতা পুলিশও সিদ্ধান্ত নিয়েছে নতুন করে ‘স্টোনম্যান’ মামলা নিয়ে ভাবনাচিন্তার, নতুন ভাবে তথ্যানুসন্ধানের। আশা করি, মামলাগুলির যৌক্তিক নিষ্পত্তির পথে এগোতে পারব আমরা।
এই বই পাঠকের মনে রোমাঞ্চ জাগাক।
রাজীব কুমার, আই. পি. এস
নগরপাল, কলকাতা
২০ ডিসেম্বর, ২০১৮
.
লেখকের কথা
একের পরে দুই। প্রথম খণ্ডের পর দ্বিতীয়। ‘গোয়েন্দাপীঠ লালবাজার’, আবার।
লেখকের দৃষ্টিকোণে ভাবলে, এ ধরনের সিরিজ লেখার ভাল-খারাপ দুইই আছে। ভাল এই, প্রথমটা পাঠকদের সমর্থন পেলে দ্বিতীয়তে হাত দেওয়ার ভরসা জোটে কিছুটা। উৎসাহ মাথাচাড়া দেয়, তা হলে দেখাই যাক লিখে। আর খারাপটা হল, আশঙ্কা। দ্বিতীয়টা যদি পাঠক-প্রশ্রয় না পায় প্রথমের মতো, অবচেতনে এই উদ্বেগ।
দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে শেষমেশ লিখে ফেলা গেল, দুই মলাটে বাঁধা পড়ল এগারোটি মামলার নেপথ্যকথা।
এই খণ্ডের মামলাগুলির সময়কাল বিস্তৃত ১৯৪৮ থেকে হালের ২০১০ পর্যন্ত। খুব পুরনো মামলা বলতে একটিই, ওই স্বাধীনোত্তর ’৪৮-এর। বাকিগুলি গত তিন দশকের সময়সীমায়।
মামলাগুলি বাছার কাজটা সহজসাধ্য ছিল না, স্বীকার্য অকপটে। লালবাজারের মহাফেজখানায় মামলার সংখ্যা তো নেহাত কম নয়। সমস্যা সংখ্যা নিয়ে নয়। সমস্যা শ’খানেক মামলার কেস ডায়েরি ঘেঁটে এমন ঘটনাগুলি বাছাই করা, যাতে বাস্তবের তদন্তপ্রক্রিয়ার অচেনা-অজানা দিকগুলোর সঙ্গে কিছুটা আলাপ করিয়ে দেওয়া যায় রহস্যপিপাসু পাঠকের। কল্পনার রহস্যগল্পের সংকলন যেহেতু নয়, যেহেতু আদতে মামলাগুলির আখ্যান ‘Police Procedural’ শ্রেণিভুক্ত, তাই আজ এবং আগামীর তদন্তশিক্ষার্থীদের ভাবনার রসদ জোগানোর একটা দায়ও ছিল বাছাইপর্বে।
দায় ছিল সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অপরাধের চরিত্রবদলের ছবিটাও তুলে ধরার। খুন-ডাকাতি-লুঠপাট বা পরিচিত ছকের চুরি-বাটপাড়িতে তো আর সীমায়িত নেই আজকের অপরাধের দুনিয়া। প্রযুক্তির প্রসারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চেহারা বদলেছে অপরাধের। বদলেছে প্রয়োগ-পদ্ধতি। বদলাচ্ছে রোজ।
সারা বিশ্বের পুলিশের কাছেই গত কয়েক দশকে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে তর্কাতীতভাবে দেখা দিয়েছে ‘সাইবার ক্রাইম’। গুলি-বন্দুক-ছুরি নিয়ে ‘হা রে রে রে’ জাতীয় ডাকাতির প্রয়োজন পড়ে না আজকের ই-মেল-হোয়াটসঅ্যাপ-ফেসবুক শাসিত পৃথিবীতে, হাতের কাছে যদি থাকে একটা ডেস্কটপ-ল্যাপটপ বা নিদেনপক্ষে একটা মোবাইল ফোন। মাউসের একটা ক্লিকে, মোবাইলের কি-প্যাডের খুচরো খুটখাটে দূরতম মহাদেশ থেকে আমার-আপনার মেল ‘হ্যাক’ হয়ে যেতে পারে যখন-তখন। নিমেষে লোপাট হয়ে যেতে পারে আজীবনের সঞ্চয়, হাতবদল হয়ে যেতে পারে আপনার যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য। প্রতারণার ফাঁদ পাতা ইন্টারনেটের ভুবনে। যাতে পা দিয়ে বিশ্বজুড়ে রোজ বহু মানুষ অসাবধানতার মাশুল গুনছেন সর্বস্বান্ত হয়ে। পরিণতি, প্রযুক্তি-প্রহরা আজকের তদন্তকারীদের সিলেবাসে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টার।
প্রযুক্তির উন্নতির সুবিধে-অসুবিধে, দুইয়ের সঙ্গেই এখন সংসার করতে হচ্ছে বাস্তবের ফেলু-ব্যোমকেশদের। নয়ের দশকের মাঝামাঝি ভারতে মোবাইল ফোন এসে যাওয়ার পর ‘ইলেকট্রনিক সার্ভেল্যান্স’-এর মধ্যস্থতায় অনেক অপরাধের কিনারা যেমন সহজতর হয়েছে, মুদ্রার অন্য দিকটাও উপেক্ষার নয়। প্রযুক্তিপটু সাইবার-অপরাধীদের কথা ছেড়েই দিলাম, নেহাতই ছিঁচকে চোরের মনেও একটা ধারণা হয়ে গিয়েছে মোবাইল ফোনের ‘কল ডিটেলস রেকর্ডস’ বা ‘ টাওয়ার লোকেশন’-এর ব্যাপারে। প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে পুলিশ যাতে নাগাল না পায়, সেই ফন্দিফিকিরের খোঁজে নিত্যদিন ব্যস্ত থাকছে অপরাধ জগতের চুনোপুঁটি থেকে রাঘববোয়ালরা। ফল? টি-টুয়েন্টির আবির্ভাব যেমন অনেকটাই বদলে দিয়েছে প্রথাসিদ্ধ ক্রিকেটের ব্যাকরণ, তদন্তের সন্ধি-সমাসও তেমন অনেকাংশে পালটে দিয়েছে সাইবারস্পেস। দেশের ইতিহাসে অন্যতম চাঞ্চল্যকর সাইবার-অপরাধের একটি কাহিনির অন্তর্ভুক্তি তাই এই বইয়ে একরকম অনিবার্যই ছিল। যেমন অনিবার্য ছিল সূচিপত্রে স্টোনম্যান মামলার ঢুকে পড়া। বহু জটিল মামলার সমাধান যেমন কলকাতা পুলিশকে ‘স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড’ অভিধা দিয়েছে, পাশাপাশি কিছু কেস তো রয়েইছে, যার সমাধানে ব্যর্থ হয়েছি আমরা সর্বস্ব উজাড় করে ঝাঁপানো সত্ত্বেও। যে তালিকায় নিঃসংশয় শীর্ষবাছাই স্টোনম্যান মামলা। যা নিয়ে কৌতূহলের জোয়ারে এতটুকু ভাটা পড়েনি ঘটনার ত্রিশ বছর পরেও। যা ঘটেছিল, যেভাবে ঘটেছিল, প্রামাণ্য বিবরণ থাকল এই খণ্ডে।
যাঁর উৎসাহ ছাড়া এই বই পাঠকের কাছে পৌঁছনো অসম্ভব ছিল, তিনি কলকাতার নগরপাল শ্রীরাজীব কুমার। যাঁকে অনিঃশেষ কৃতজ্ঞতাই জানাতে পারি শুধু। পারিবারিক দায়িত্ব একপ্রকার বিসর্জন দিয়েই বিনিদ্র রাতের লেখায় শর্তহীন সমর্থন পেয়েছি স্ত্রী-পুত্র-কন্যার। ধন্যবাদ দেওয়ার সম্পর্ক নয়। দিলাম না।
এর বেশি আর কী লেখার? মৌলিকতার ন্যূনতম দাবি নেই এই বইয়ের। যা আছে, দ্বিমুখী উদ্দেশ্য। এক, গ্রন্থিত রাখা গোয়েন্দাপীঠ লালবাজারের রহস্যভেদের ঐতিহ্য। দুই, তদন্তপথের কিছু দিকনির্দেশ লিপিবদ্ধ রাখা ভাবীকালের স্বার্থে।
উদ্দেশ্য আদৌ কিছুমাত্র সাধিত হল কি না, বিচার পাঠকের। দিনের শেষে পাঠকই পরম।
১ জানুয়ারি, ২০১৯
কলকাতা
২.০১ ডক্টর জেকিল, না মিস্টার হাইড?
[রোশনলাল মামলা
একাধিক অফিসার যুক্ত ছিলেন। প্রাপ্ত নথি থেকে নিশ্চিতভাবে যাঁদের নাম জানা যায় না।]
—‘কেয়া ফেকতা হ্যায় বাবু? কেয়া ফেকতা হ্যায়?’
দৃশ্যটা দেখে সহসা থমকে গিয়েছিলেন ত্রিলোচন। কম দিন তো হল না এ তল্লাটে। এই জায়গাটা বরাবরই নির্জন। আজ যেন একটু বেশিই শুনশান, হাঁটতে হাঁটতেই মনে হয়েছিল ত্রিলোচনের। গত রাতের তুলকালাম বৃষ্টির জন্য? লোক একটু কম যেন? অন্তত অন্যদিনের তুলনায়?
দক্ষিণ কলকাতার বহুপরিচিত সরোবর-প্রাঙ্গণ। সাধারণের কথ্যভাষায়, লেক। যেখানে দৈনিক প্রাতঃভ্রমণে আসেন নগরবাসীরা। যাঁদের স্বাস্থ্যরক্ষার তাগিদের সাক্ষী থাকাটা একরকম অভ্যাসেই পরিণত হয়েছে ত্রিলোচনের।
আজ থেকে বেশ কয়েক বছর আগে লেক এলাকার নিরাপত্তারক্ষীর চাকরিটা পেয়েছিলেন। সেই থেকে একই রুটিন দৈনন্দিন। সূর্য আড়মোড়া ভাঙতে না ভাঙতেই বেরিয়ে পড়া, লেকের বিস্তীর্ণ এলাকায় পাক দেওয়া পদব্রজে। দিনের পর দিন একই কাজ একই রাস্তায় বছরের পর বছর করে গেলে যা হয়, চোখ বেঁধে দিলেও এই রোজকার টহলদারি মোটেই কষ্টসাধ্য হবে না, জানেন ত্রিলোচন।
যেখানে থমকে গেলেন ত্রিলোচন, সেই জায়গাটা লেকের এক প্রান্তে। এই সীমা পর্যন্ত খুব স্বল্পসংখ্যক হাতেগোনা মানুষই আসেন। বস্তুত, সচরাচর কেউ আসেনই না এতদূর। সংগত কারণ ছিল ত্রিলোচনের অবাক হওয়ার। উনি কে? ওই ভদ্রলোক? বেঞ্চে বসেছিলেন এক মহিলার পাশে। হঠাৎ উঠে এদিক-ওদিক তাকালেন, হাতে একটা বড় চটের ব্যাগ নিয়ে দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলেন লেকের ধারে। ফের সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালেন চারপাশে।
ব্যাগটা ফেলতে যাচ্ছেন জলে? ভদ্রলোক ওভাবে চারদিক দেখছেন কেন? উদ্বেগ কেন এত চোখেমুখে? কী ফেলতে যাচ্ছেন? কী আছে ব্যাগে? ত্রিলোচন থমকান দেখে। সন্দেহ হয়। হাঁক দেন বাজখাঁই গলায়, ‘কেয়া ফেকতা হ্যায় বাবু, কেয়া ফেকতা হ্যায়?’
‘ওরে বাবা দেখ চেয়ে, কত সেনা চলেছে সমরে!’
এ দৃশ্য আগে দেখেছে কলকাতা? স্রেফ একটা মামলার জন্য এহেন যুদ্ধং দেহি সাজ? টগবগ টগবগ ধ্বনি আলিপুর আদালতের সামনের রাস্তা জাজেস কোর্ট রোডে। ঘোড়াপুলিশ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে রাজপথে। সন্ত্রস্ত পথচারীরা দেখছে নিরাপদ দূরত্ব থেকে। পুলিশের গাড়ি এসে থামছে একে একে। আদালত প্রাঙ্গণে ‘পজিশন’ নিচ্ছেন উর্দিধারীরা। আজ রায় ঘোষণা হবে। ‘জাজমেন্ট ডে’।
‘ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই’ অবস্থা এজলাসে। বাইরের রাস্তাও জনাকীর্ণ। আরও অনেকে ঢুকতে চান, দেখতে চান, শুনতে চান। কোর্ট চত্বরের মূল প্রবেশপথ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে পুলিশ। লালবাজারের তরফে পূর্ণাঙ্গ পুলিশি বন্দোবস্ত করা হয়েছে শ’য়ে শ’য়ে উৎসাহী জনতাকে দূরবর্তী রাখতে। দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে নেহাতই স্বল্পপরিসরের ওই এজলাস, অবাধ প্রবেশের অনুমতি দেওয়া মানে অনর্থকেই আমন্ত্রণ।
তর সইছে না জনতার। সত্যি কথা বলতে, পুলিশেরও। আর কত দেরি? যখন বিচারক পড়তে শুরু করলেন দীর্ঘ রায়, অনন্ত অপেক্ষার পর যখন পৌঁছলেন শাস্তিদানের অনুচ্ছেদে, এজলাসের দখল নিয়েছে পিনপতন নীরবতা। বেলা তখন প্রায় দ্বিপ্রহর।
‘Taking into account the facts and circumstances of the case…’
এ কাহিনি প্রায় সত্তর বছর আগের। সন ১৯৪৮, স্বাধীনতার সঙ্গে তখনও আলাপ-পরিচয়ের পর্ব চলছে দেশের।
রহস্যভেদের রোমান্স-রোমাঞ্চ অমিল এ আখ্যানে। তবু আলোচ্য মামলার মতো চাঞ্চল্যকর এবং বহুচর্চিত কেস এদেশের অপরাধ-ইতিহাসে খুব বেশি নেই।
পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে যাঁরা অশীতিপর, তাঁদের স্মরণে থাকলেও থাকতে পারে এই মামলা। স্মরণে থাকতে পারে ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে সমসাময়িক জল্পনা-কল্পনা-চৰ্চার তীব্রতা। শুধু সমসময়ই বা লিখি কেন, দেশের বিভিন্ন পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আজও যখনই আলোচিত হয় স্বাধীনোত্তর যুগের সাড়া-জাগানো মামলাগুলির ইতিবৃত্ত, অবধারিত উল্লেখিত হয় সাত দশক আগের এই ঘটনা।
সমস্যা হল, মামলার বিস্তারিত নথিপত্রের অনেকটাই নষ্ট হয়ে গেছে সময়ের প্রকোপে। একাধিক অফিসার বিভিন্ন পর্যায়ে তদন্তের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। যাঁদের কয়েকজনের নাম নির্দিষ্ট ভাবে জানা যায় না। যতটুকু জানা যায় এই মামলা নিয়ে পত্র-পত্রিকায় পদস্থ অফিসারদের লেখালেখি থেকে, যতটুকু উদ্ধার করা যায় শতচ্ছিন্ন কেস ডায়েরির হলুদ হয়ে-আসা পাতাগুলির পাঠযোগ্য অংশ থেকে, পেশ করলাম।
কৃষ্ণহরি শর্মা। বয়স যখন কুড়ি, দার্জিলিং জেলার আর্মড পুলিশে যোগ দিয়েছিলেন। বিয়ে করেছিলেন তারও বছর তিনেক পরে। যশোদাদেবীকে। এই দম্পতির তিন সন্তান। দুই মেয়ে, এক ছেলে। বড়মেয়ের নাম মণি। ছোটমেয়ে বেলা। সবার ছোট হল অমল।
দীর্ঘ কর্মজীবনের মধ্যভাগে কৃষ্ণহরিকে গ্রাস করল বিবিধ রোগব্যাধি। ১৯৪১-এ যখন মারা গেলেন, বড়মেয়ে মণি তখন একুশ বছরের সুন্দরী যুবতী। দার্জিলিংয়ে কলেজের পাট চোকার পর নার্সিং কোর্সে ভরতি হয়েছেন সদ্য। ছোটমেয়ে বেলা তখন উনিশ। অমলের সবে ষোলো পেরিয়েছে।
স্বামীর মৃত্যুর পর সপরিবারে কলকাতায় চলে এলেন যশোদা। কলকাতায় যশোদার এক বোন থাকতেন। নাম ডলি। যাঁর বিয়ে হয়েছিল কিরণ দে নামের এক বঙ্গসন্তানের সঙ্গে। সম্ভ্রান্তবংশীয় কিরণ পদস্থ চাকুরে ছিলেন। সানন্দে আশ্রয় দিয়েছিলেন যশোদা এবং তাঁর তিন সন্তানকে। অমল এবং বেলা কলকাতার কলেজে ভরতি হল। মণির নার্সিং-এর পড়াশুনো চালু হল নতুন উদ্যমে। বঙ্গীয় জীবনধারার সঙ্গে দ্রুত অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন যশোদা। মণি-বেলা-অমলও।
নিরুদ্বেগ জীবন কাটল কয়েক বছর। উদ্বেগের সূত্রপাত হল ১৯৪৬ সালে, যখন অমলের ফুসফুসে ধরা পড়ল যক্ষ্মা রোগের সংক্রমণ। যাদবপুর হাসপাতালে চিকিৎসায় অমলের কিছুটা স্বাস্থ্যোদ্ধার হওয়ায় যশোদা কিঞ্চিৎ স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন বটে, কিন্তু সে স্বস্তি স্থায়ী হল স্বল্পকালই। ’৪৬-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বেঘোরে প্রাণ হারালেন কলেজপড়ুয়া অমল। একমাত্র পুত্রের অকালমৃত্যুতে যশোদা সাময়িক বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। মণি এবং বেলা আপ্রাণ শুশ্রূষায় ক্রমে স্বাভাবিকতায় ফেরালেন মা-কে।
যশোদার বোন ডলি এর কিছুদিন পরেই মারা গেলেন মাত্র সপ্তাহখানেকের জ্বরে। মানসিকভাবে আরও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লেন যশোদা। ডলির স্বামী কিরণ আদ্যন্ত ভদ্রলোক ছিলেন। মুখে কখনও কিছু বলেননি, তবে ডলির মৃত্যুর পর আশ্রিতা হয়ে সপরিবারে তাঁর বাড়িতে বসবাস করার অস্বস্তি ক্রমে গ্রাস করল যশোদাকে। কিন্তু গেলেও যাবেনই বা কোথায়? কে জায়গা দেবে সপরিবারে দুই মেয়েকে নিয়ে থাকার? বাড়ি ভাড়া করে থাকার মতো আর্থিক সংগতি নেই। নিরুপায় আশ্রিতার দিনগত পাপক্ষয়কেই ভবিতব্য মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কী আর?
’৪৬ সালেরই শেষ দিকে আলিপুর মিলিটারি হাসপাতালে নার্সের চাকরি পেলেন মণি। বেতন ভদ্রস্থ। যশোদা ভাবলেন, মানসিক কষ্ট কমাটা দুষ্কর, অন্তত অর্থকষ্টটা এবার কিছুটা কমবে।
মিলিটারি হাসপাতালে ইএনটি বিভাগে নার্স হিসাবে নিযুক্ত হলেন মণি। ওই বিভাগের দায়িত্বে তখন মেজর রোশনলাল সিং। মণি প্রথম দর্শনেই প্রেমে পড়লেন আপাদমস্তক, রোশনলালের চোখে দেখলেন নিজের সর্বনাশ।
দোষ দেওয়া যায় না মণিকে। একটা অমোঘ আবেদন ছিল রোশনলালের ব্যক্তিত্বে, যার চৌম্বকীয় আকর্ষণ উপেক্ষা করা কঠিন হত মেয়েদের পক্ষে। কাহিনি আরও অগ্রসর হওয়ার আগে, আসুন, আলাপ করিয়ে দিই রোশনলালের সঙ্গে।
রাজা রোশনলাল সিং সুয়েজভান— পুরো নাম। কাশ্মীরের মহারাজা সুয়েজভান সিং-এর বংশজাত। বরাবরই প্রখর মেধাবী। সসম্মানে ডাক্তারি পাশ করার পর যুবক রোশনলাল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যোগ দিয়েছিলেন Indian Army Medical Corps-এ। অসামান্য কর্মদক্ষতা পথ সুগম করেছিল দ্রুত পদোন্নতির। ডাক্তার রোশনলাল মেজর পদে উন্নীত হয়েছিলেন ১৯৪৬ সালে। কলকাতার আলিপুরে সেনাবাহিনীর হাসপাতালে E. N. T. বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব পেয়েছিলেন।
রোশনলালের চরিত্রের কাটাছেঁড়ায় মনে পড়তে বাধ্য ১৮৮৬ সালে রচিত রবার্ট লুইস স্টিভেনসনের সেই কালজয়ী উপন্যাস, ‘Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde’।
Dr. Henry Jekyll, শান্ত, ধীরস্থির, হৃদয়বান এক চিকিৎসক। যিনি দিনের বেলায় সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কিন্তু এক রাসায়নিক তরলের প্রভাবে রাত্রিবেলা জেগে ওঠে যাঁর অন্য সত্তা। Dr. Jekyll হয়ে ওঠেন Mr. Edward Hyde, যিনি স্বভাবে-আচারে-আচরণে Dr. Jekyll-এর সম্পূর্ণ বিপ্রতীপে। নৃশংস-বিবেকবর্জিত-দয়ামায়াহীন এক খুনি। একই মানুষ, দ্বৈত সত্তা।
রোশনলালও ছিলেন তা-ই। এক গবেষণাযোগ্য চরিত্র। একই অঙ্গে দ্বৈত রূপ। দীর্ঘদেহী সুঠাম চেহারার তরুণ ডাক্তার। সুদর্শন। চশমার পিছনে বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ। চলনে-বলনে-পোশাকে-আশাকে দৃশ্যমান, রাজরক্ত বইছে এই লোকটির শরীরে।
এক একজন থাকেন, যে-কোনও সামাজিক সমাবেশে হাজির হলেই সব আলো কেড়ে নেন অবলীলায়। রোশনলাল ছিলেন সেই গোত্রের। সাহিত্য বলুন বা বিজ্ঞান, দর্শন বলুন বা নৃতত্ত্ব, যে-কোনও বিষয়ে পাণ্ডিত্য ছিল প্রশ্নাতীত। যখন কথা বলতেন মার্জিত বাচনভঙ্গিতে, লোকে শুনত মন্ত্রমুগ্ধ। যখন রোগীর চিকিৎসায় নাওয়া-খাওয়া ভুলে হাসপাতালে কাটিয়ে দিতেন রাতের পর রাত, সহকর্মীদের শ্রদ্ধা-সম্ভ্রম কুড়িয়ে নিতেন অনায়াসে।
নিজের লেটারহেডে ছাপিয়ে রেখেছিলেন, ‘Worship God by servicing the ailing humanity’। দুঃস্থ মানুষকে দানধ্যান করতেন নিয়মিত। মদ-সিগারেটের সঙ্গে কোনওরকম সংস্রব ছিল না নিত্যদিন পূজাপাঠ করা রোশনলালের। হুবহু ড. জেকিল। যাঁর প্রেমে না পড়ে উপায় ছিল না মণির। জানতেন না প্রেমিকপুরুষের দ্বৈতসত্তার কথা। যখন জেনেছিলেন, দেরি হয়ে গিয়েছিল বিস্তর।
মণির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ল রোশনলালের। মানসিক এবং শারীরিক। ’৪৬-এর ডিসেম্বরে মণি সন্তানসম্ভবা হলেন। এবং রোশনলালকে বললেন, ‘এবার বিয়েটা করে নেওয়া দরকার।’ যখন বলেছিলেন, জানতেন না রোশনলালের গোপন করে যাওয়া দুটি তথ্য। এক, রোশনলাল বিবাহিত। স্ত্রী-র নাম কৌশল্যা। দুই, ওঁদের একটি পুত্রসন্তানও বর্তমান। নাম, সুদর্শন কুমার।
মণির বিবাহ-প্রস্তাবে রোশনলাল রাজি হলেন এক কথায়। নির্দিষ্ট দিনে এক বন্ধুর বাড়িতে উপস্থিত হলেন মণিকে নিয়ে। এক পুরোহিত বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ করলেন, সাক্ষী রইল অগ্নিকুণ্ড। মণি যারপরনাই অবাক হলেন বৈবাহিক ক্রিয়াকর্মের রীতিনীতিতে। আত্মীয়স্বজনের বিয়েতে আশৈশব দেখে এসেছেন হিন্দু ধর্মমতে বিয়ের পরিচিত আচারবিধি। এ তো আলাদা সম্পূর্ণ!
রোশনলাল স্মিতহাস্যে জানালেন, হিন্দুমতে বিবাহের আয়োজন যথেষ্ট সময়সাপেক্ষ। ব্যয়বহুলও। তার চেয়ে আপাতত এই ভাল। আর্যসমাজ মতে এভাবেই হয় বৈবাহিক প্রক্রিয়া। মণি তখন মোহাচ্ছন্ন রোশনলালের প্রেমে। প্রিয়তম পুরুষের প্রতি সন্দেহের ন্যূনতম অবকাশই নেই।
মণি যখন প্রশ্ন করলেন বিয়ের আইনসিদ্ধ রেজিস্ট্রি নিয়ে, রোশনলাল ফের সহাস্যে বললেন, ‘ওটা তো যে-কোনওদিন করে নেওয়া যাবে। সত্যি বলো তো, তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো না?’ আবেগবিহ্বল মণি আনন্দাশ্রু ব্যয় করলেন কিছু। সমর্পণ সম্পূর্ণ হল।
পরের বছর, ’৪৭-এ জন্ম হল রোশনলাল-মণি-র শিশুপুত্রের। নাম রাখা হল মুন্না। ’৪৮-এ ফের গর্ভবতী হলেন মণি। এবার কন্যাসন্তান। মুন্নি। ’৪৭-এর মাঝামাঝি রোশনলাল ফ্ল্যাট ভাড়া করলেন ৪/ডি মতিলাল
নেহরু রোডে একটি বাড়ির চারতলায়। যশোদা-মণি-বেলা উঠে এলেন দেশপ্রিয় পার্কের থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বের
সেই ফ্ল্যাটে। পরাশ্রিত থাকার থেকে মেয়ে-জামাইয়ের সংসারে দিনাতিপাতই শ্রেয়তর মনে করলেন যশোদা।
রোশন-মণির সম্পর্কে চিড় ধরা শুরু দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের কিছুকাল পর থেকে। মণির সঙ্গে রোশনলাল ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন স্রেফ শরীরী আকর্ষণে। মন ছিল বহু আলোকবর্ষ দূরে। আর্যসমাজ মতে বিয়ের ছদ্মচিত্রনাট্য সাজিয়েছিলেন মণি সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়ায়।
মানসিক সংযোগ না থাকলে ‘আদিম রিপু’-র তাড়না একটা সময় স্তিমিত হয়ে আসেই। শরীরী মোহ কাটিয়ে ওঠার পরই নিজমূর্তি ধরলেন রোশনলাল। বদলির নির্দেশ এল রাঁচির নামকুম হাসপাতালে। মণি এবং দুই সন্তানকে নিয়ে পাড়ি দিলেন রাঁচি। যেখানে অন্য রোশনলালকে চিনতে শুরু করলেন মণি। যিনি আর ডক্টর জেকিল নন। সর্বার্থেই মিস্টার হাইড।
প্রতি পদে রোশনলাল বুঝিয়ে দিতে লাগলেন, মাঝে মাঝে শরীরী চাহিদা মেটানোর ভোগ্যবস্তুর বেশি মর্যাদা তিনি মণিকে দিতে নারাজ। মণি যখনই বিয়ের রেজিস্ট্রির কথা তুলতেন, নির্বিচার গালিগালাজ করতেন রোশনলাল। সমাজের চোখে সুভদ্র হিসাবে পরিচিত ডাক্তারবাবুর মুখ থেকে অকথা-কুকথার বন্যা বয়ে যেত। কথায় কথায় মণির গায়ে হাত তোলা অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল রোশনলালের। একটা পর্যায়ের পর মণি বুঝে গিয়েছিলেন, বিবাহিতা স্ত্রী-র স্বীকৃতি পাবেন না কোনওদিনই। কানাঘুষোয় শুনতেন অন্য একাধিক নারীর সঙ্গে স্বামীর ঘনিষ্ঠতার কথা। এমনও হত, রাতের পর রাত বাড়িই ফিরতেন না রোশনলাল। প্রশ্ন করলে বরাদ্দ থাকত উপেক্ষা এবং ঔদাসীন্য।
বিনিদ্র রাতে মণি চোখের জল ফেলতেন আর ভাবতেন, কী পরিচয়ে তা হলে দিন কাটাচ্ছেন রোশনলালের সঙ্গে? সোজা বাংলায়, রক্ষিতাই তো! জীবন কি এ ভাবেই কাটবে, অবহেলা-অনাদর-অত্যাচারের গ্লানি মুখ বুজে সহ্য করে? ছেলেমেয়ে এখনও দুধের শিশু। তাদের পরিচর্যার দায়িত্ব সামলে নার্সের চাকরির চেষ্টা করাটাও অসম্ভবের পর্যায়েই। আরও অসম্ভব, কারণ, এরই মধ্যে ফের সন্তানসম্ভবা হয়ে পড়েছেন।
পরিস্থিতির চাপে দিশেহারা মণি দাঁতে দাঁত চেপে তবু মেনে নেওয়ার এবং মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেই যাচ্ছিলেন। এবং হয়তো করেই যেতেন, যদি না এক সন্ধেয় হঠাৎই দেখে ফেলতেন ওঁদের দু’জনকে।
বেশ কয়েক মাস ধরে পাওলিন নামের এক অতীব সুন্দরী মহিলার গলার সংক্রমণের চিকিৎসা করছিলেন রোশনলাল। রাঁচির টেলিফোন এক্সচেঞ্জে অপারেটরের কাজ করতেন তেইশ বছরের পাওলিন। মাঝেমধ্যে রোশন-মণির ফ্ল্যাটেও আসতেন। মুন্না-মুন্নির জন্য উপহার আনতেন। রান্না করেও আনতেন ভালমন্দ।
এমনই এক সন্ধেয় এসেছেন পাওলিন। ঘণ্টাদুয়েক গল্পগুজবের পর বেরলেন। রোশনলাল কিছুটা এগিয়ে দিতে গেলেন পাওলিনকে। বেশ কিছুক্ষণ পরও যখন ফিরলেন না, কৌতূহলবশত মণি বাইরের ঘরের জানালায় চোখ রাখলেন। এবং আধো অন্ধকারেও স্পষ্ট বুঝলেন, কোয়ার্টারের গেটের কাছে রোশনলাল আর পাওলিন পরস্পরের আলিঙ্গনবদ্ধ। দু’জনের ঠোঁটের মধ্যে ব্যবধান অন্তর্হিত।
সে-রাতে বাদানুবাদ হল রোশন-মণির। একটা সময় রোশনলাল নিরুত্তাপ গলায় বললেন, ‘পাওলিন আমার বোনের মতো। ভাই-বোনে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়ায় দোষের কিছু নেই। নিজের মান্ধাতার আমলের চিন্তাভাবনা বদলাও।’
স্বামীর এহেন ব্যাখ্যায় বাক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন মণি। পরনারীতে রোশনলালের আসক্তির ব্যাপারে আন্দাজ করতেন মণি, সন্দেহও। কিন্তু নিজের ফ্ল্যাটের চৌহদ্দির মধ্যেই যখন চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন ঘটল, মণি মনস্থির করে ফেললেন।
পরের দিন ছেলেমেয়েকে নিয়ে রওনা দিলেন কলকাতায়। উঠলেন মতিলাল নেহরু রোডের সেই ভাড়ার ফ্ল্যাটে, যেখানে যশোদাদেবী বসবাস করতেন ছোটমেয়ে বেলার সঙ্গে। মণির মুখে সব শুনলেন যশোদা। অদৃষ্টকে দোষারোপ আর অশ্রুপাত ছাড়া কী-ই বা করার ছিল প্রৌঢ়ার?
কূটবুদ্ধির অভাব আছে, রোশনলালের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ তাঁর চরম শত্রুর পক্ষেও করা অসম্ভব ছিল। মণি কলকাতায় ফিরে যাওয়ার পর ছক কষলেন বরফশীতল মস্তিষ্কে। অসম্ভব ইমেজ-সচেতন মানুষ ছিলেন রোশনলাল। জানতেন, মণি যদি তাঁর কীর্তিকলাপের ব্যাপারে আলোচনা করেন পরিচিত মহলে, সামাজিক প্রতিপত্তিতে আঁচড় পড়তে পারে। তাই মণির আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখাটাই আপাতত প্রধান কর্তব্য বলে স্থির করলেন। দুটো চিঠি লিখলেন মণিকে। পাঁচ দিনের ব্যবধানে। অগস্টের ১৪ এবং ১৯ তারিখে। যা লিখলেন, তুলে দিচ্ছি অংশবিশেষ।
১৪.০৮.৪৮
‘প্রিয়তমা মণি,
… তুমিই আমার জীবন, আমার সব কিছু। তুমি আমাকে চিঠি লিখছ না কেন? তোমার চিঠি না পেলে আমার নিজেকে শূন্য মনে হয়। ডার্লিং প্লিজ়, এবারের মতো আমায় মাফ করে দাও। দেখবে, আমি অনেক বদলে গেছি। ভুল বুঝো না আমায়। তোমার কোনওরকম ক্ষতি হয় এমন কাজ আমি কখনও করব না। মন থেকে প্লিজ় সমস্ত সন্দেহ দূর করে দাও… দেখবে আমরা আগের মতো সুখী জীবন কাটাতে পারব। আমাদের তৃতীয় সন্তান কিছুদিন পরেই পৃথিবীতে আসতে চলেছে। অন্তত তার কথা ভেবে সমস্ত ভুল বোঝাবুঝিকে চলো মুছে ফেলি আমরা…
তোমার রোশন’
১৯.০৮.৪৮
‘ডার্লিং,
…তোমাকে আমি আর কতবার বলব যে আমি তোমাকে মিথ্যে বলার কথা ভাবতেও পারি না। আমি তোমাকে কখনও ঠকাব না। আমি তোমাকে ভালবাসি… এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভালবাসব।
আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় যে বিয়েতে রেজিস্ট্রিটাই সব? বিয়ের আসল জিনিস তো ভালবাসা। রেজিস্ট্রি বিয়েতে স্বামী-স্ত্রী একে অন্যকে ছেড়ে চলে যেতে পারে, ডিভোর্স করতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ভালবাসার যে বিয়ে, তাতে কখনও ছাড়াছাড়ি হয় না। আমার কথাগুলো মন দিয়ে ভেবে দেখো।
তোমারই রোশন’
এই কুম্ভীরাশ্রুতে যে বিশেষ বরফ গলছে না, বুঝতে পারছিলেন রোশনলাল। একটি চিঠিরও উত্তর দিচ্ছিলেন না মণি। এবং উদ্বেগ বাড়ছিল রোশনলালের। সিদ্ধান্ত নিলেন কলকাতায় আসার। রাঁচির সেনা হাসপাতালের চাকরিটা ছাড়লেন। কলকাতায় এসে যোগ দিলেন লেক মিলিটারি হাসপাতালে। উঠলেন হাসপাতালের নির্দিষ্ট কোয়ার্টারেই। কলকাতায় পৌঁছনোর সন্ধেতেই গেলেন মতিলাল নেহরু রোডের ফ্ল্যাটে মণির সঙ্গে দেখা করতে। এবং বুঝলেন, যা আশঙ্কা করছিলেন, সত্যিই। এ মণি আর সেই মণি নয়, যিনি স্বামীর মিষ্টি কথার জাদুতে আগের মতো মোহাবিষ্ট হয়ে পড়বেন।
রোশনলালের প্রতি মণির ভালবাসা ছিল নিখাদ। স্বামীর বিশ্বাসভঙ্গে চিন্তাতীত আঘাত পেয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু সে আঘাত মণির মানসিক কাঠিন্যের বুনিয়াদ অনেকটাই পোক্ত করে দিয়েছিল। রোশনলালকে বললেন, প্রায় তিন বছর স্বামী-স্ত্রী হিসাবে একত্রে বসবাসের পর, দুই সন্তানের জন্ম দেওয়ার পর এবং তৃতীয়বার সন্তানসম্ভবা হওয়ার পরও যদি বিয়েকে আইনি বৈধতা দেওয়া নিয়ে এতটা দ্বিধাগ্রস্ত থাকেন রোশনলাল, তা হলে তো এই সম্পর্কের কোনও মানেই দাঁড়ায় না। পরিস্থিতি যে দিকে গড়াচ্ছে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে এই অনাচারের বিচার চাওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না আর। নিজের মানসম্মানের দায়িত্ব তখন রোশনলালকে নিজেকেই নিতে হবে।
রোশনলাল সব শুনলেন চুপ করে। এই প্রথম স্বামীর শরীরী ভাষায় অনুতাপের চিহ্ন দেখলেন মণি। দেখলেন, চোখ আর্দ্র হয়ে এসেছে রোশনলালের। মণিকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন, ‘বেশ, তুমি যা চাইছ, তা-ই হোক। এতে যদি তুমি শান্তি পাও, তবে তা-ই হোক। আমি রেজিস্ট্রেশনের দিনক্ষণ ঠিক করছি। কাশ্মীরের বাড়িতে আজই টেলিগ্রাম করব। আমাদের রাজবাড়িতেই রেজিস্ট্রেশন হবে বিয়ের। তারপর ধুমধাম করে অনুষ্ঠান। তুমি শুধু আমাকে আগের মতোই ভালবেসো।’ শোনামাত্র মণি কেঁদে ফেললেন স্বামীর বুকে মাথা রেখে। প্রেম বড় বিষম বস্তু।
রোশনলাল ভক্তিনিষ্ঠ প্রণাম করলেন শাশুড়িকে। চোখের জল বাধা মানল না যশোদারও। দিদির মানসিক কষ্টের অবসানের সম্ভাবনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন বেলাও।
দিনক্ষণ স্থির হল কাশ্মীর যাওয়ার। মণি যখন মা-কে প্রণাম করে বেরচ্ছেন রোশনলালের সঙ্গে, যশোদাদেবী ঘোরতর দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি, মেয়ের সঙ্গে এই তাঁর শেষ দেখা।
হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে রোশনলাল মণিকে বললেন, ‘চলো দু’-একদিনের জন্য পুরী ঘুরে আসি। সেখান থেকে কাশ্মীর যাব।’ হঠাৎ এই প্ল্যান পরিবর্তন? জানতে চাইলেন মণি। রোশন হাসলেন, ‘তুমি কি এখনও আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না? আমরা কোথাও কখনও একসঙ্গে বেড়াতে যাইনি। তাই ভাবলাম, দু’দিন সমুদ্রের ধারে একটু সময় কাটাই দু’জনে। আমি তোমাকে সারপ্রাইজ় দিতে চেয়েছিলাম। তুমি রাজি হবে না জানলে টিকিট কাটতাম না।’
মণি রাজি হলেন রোশনের কথায়। সন্দেহ হয়েছিল কি কিছু? হয়তো হয়েছিল। তবু রাজি হয়েছিলেন, বহুকাঙ্ক্ষিত রেজিস্ট্রেশনের ব্যাপারে পাছে মত বদলান রোশন, সেই আশঙ্কাতেই সম্ভবত। ট্রেনে উঠে বসলেন দু’জনে।
পুরী। আজকের পুরীর সঙ্গে সে-কালের পুরীর তফাত ছিল আকাশপাতাল। শহরের যত্রতত্র হোটেল গজিয়ে ওঠেনি গায়ে গা লাগিয়ে। হরেক পশরা সাজিয়ে তট বরাবর মাথা তোলেনি অসংখ্য দোকানপাট। পর্যটকদের ভিড়ে তখন অষ্টপ্রহর থইথই করত না সমুদ্রতট। নির্জনতাই নিরঙ্কুশ।
সমুদ্রের ধারেই একটি সাদামাটা ছিরিছাঁদহীন হোটেলে ঘর ভাড়া নিলেন রোশনলাল। হোটেলের রেজিস্টারে মিথ্যে নাম-ঠিকানা লিখলেন নিজের আর মণির।
সমুদ্রতীরে পাশাপাশি বসে সন্ধেটা দিব্যি কাটল দু’জনের। হোটেলে ফেরার আগে রোশন প্রস্তাব দিলেন, ‘চলো, একটু হেঁটে আসি।’
মণি তখন আট মাসের গর্ভবতী। বালিপথ ধরে হাঁটাহাঁটির ইচ্ছে ছিল না বিশেষ। তবু রোশনকে বিমুখ করতে মন চাইল না। স্বামীর হাত ধরে ধীরপায়ে হাঁটা দিলেন। যখন ফিরে আসছেন, পেটে ব্যথা শুরু হয়েছে তীব্র। রোশন যন্ত্রণাকাতর স্ত্রী-কে ভরসা দিলেন, ‘এ সময় এমন হয়। এই অবস্থায় এতটা না হাঁটলেই বোধহয় ভাল হত। আমারই দোষ। যাক গে, চিন্তা কোরো না। স্বামী যখন ডাক্তার, চিন্তা কীসের? হোটেলে ফিরেই ব্যথা কমার ওষুধ দিচ্ছি।’
ওষুধ দিলেন রোশনলাল। ডাক্তারি ব্যাগ থেকে বার করলেন ইনজেকশন। বিছানায় শুয়ে তখন যন্ত্রণায় ছটফট করছেন মণি, ‘কই, ওষুধটা দাও, খুব কষ্ট হচ্ছে!’ মণির হাতে সূচ ফোটালেন রোশনলাল। সূচ বেয়ে তরল প্রবেশ করল মণির শরীরে। ছড়িয়ে গেল শিরা-উপশিরায়। মরফিয়া!
রোশনলাল মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন মণির, ‘ওষুধ পড়েছে, দেখো এবার, যন্ত্রণা কমবে। ঘুম এসে যাবে।’
ঘুম এল মণির। গভীর ঘুম। রোশনলাল নিজের গলার স্কার্ফটা খুললেন। পেঁচিয়ে ধরলেন ঘুমন্ত মণির গলায়। সর্বশক্তি দিয়ে। শ্বাসরোধ করে খুন। একটা নয়, দুটো। মণির গর্ভস্থ সন্তানের দিনের আলো দেখার সময় তো হয়েই এসেছিল প্রায়।
রাত বাড়তে মণির দেহ একটা বেডশিটে মুড়ে বেরলেন ঘর থেকে। নিরাপত্তারক্ষীর বালাই থাকে না এসব সস্তার হোটেলে। অর্ধেক ঘরও খালি পড়ে থাকে। কেউ কারও খোঁজ রাখে না। নিরাপদে বেরিয়ে গেলেন গেট দিয়ে, দেহ পুঁতে দিলেন সমুদ্রতটে বালির স্তূপের নীচে। যেটা চিহ্নিত করে রেখেছিলেন বিকেলেই। মণির স্লিপার, চুড়ি, মুক্তোর নেকলেস এবং ইনজেকশনের সিরিঞ্জ ফেলে দিলেন হোটেল-সংলগ্ন একটা মজে যাওয়া কুয়োয়।
ফিরে এলেন ঘরে, এবং নিজের জিনিসপত্র নিয়ে সন্তর্পণে বেরিয়ে গেলেন হোটেল থেকে। রাত তখন সোয়া তিনটে। কোনও সাক্ষী থাকল না গভীর রাতের অন্তর্ধানের। সমুদ্র ছাড়া কে-ই বা জেগে থাকে ওই নিশুত রাতে?
রোশনলাল ফিরে এলেন কলকাতায়। মতিলাল নেহরু রোডের ফ্ল্যাটে গেলেন তারও সপ্তাহখানেক পরে। জামাইয়ের সঙ্গে মেয়েকে না দেখে যশোদা অবাক, ‘ভালয় ভালয় সব মিটে গেছে তো? মণি কই?’
—ওকে কাশ্মীরেই রেখে এলাম কিছুদিনের জন্য।
—কেন?
রোশনলাল বোঝানোর চেষ্টা করলেন যশোদাকে, যত শীঘ্র সম্ভব কলকাতায় ফিরিয়ে আনবেন মণিকে। বললেন, বিয়ের পর নববধূর মুখই দেখেননি তাঁর মা। তা ছাড়া মায়ের শরীরটা একেবারেই ভাল যাচ্ছে না। গিয়েই চলে এলে বড় বিসদৃশ দেখায়। শত হোক, রাজকুলবধূ, সামাজিকতারও দায় থাকে একটা। দায় থাকে আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে ন্যূনতম পরিচিতির।
দিনের পরে দিন যায়। সপ্তাহ যায়। আশঙ্কা আর অস্বস্তি ক্রমশ অসহনীয় হয়ে উঠছিল যশোদার। একদিন রোশনলালকে চেপে ধরলেন, ‘মণিকে নিয়ে এসো এবার। আমার কিচ্ছু ভাল লাগছে না।’
—আর সপ্তাহখানেক পরে কাজের চাপ কমলেই নিয়ে আসব। আপনি অযথা চিন্তা করছেন। আমাদের বাড়িতে আপনার মেয়ের কোনও অযত্ন হবে না, নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।
নিশ্চিন্ত থাকতে বললেই কি আর থাকা যায়? যশোদা পালটা প্রশ্ন করলেন, ‘বেশ তো, কিন্তু চিঠি লিখছে না কেন? এতদিন হয়ে গেল, একটা চিঠিও লিখবে না মেয়ে? সেই মেয়ে, যে মা-অন্ত প্রাণ একরত্তি বয়স থেকে?’
এ প্রশ্নের উত্থাপন একটা সময় অবধারিতই, বিলক্ষণ জানতেন রোশনলাল। প্রস্তুত রেখেছিলেন উত্তর।
—আসলে কী হয়েছে জানেন মা, কাশ্মীরের নিয়ম বাকি দেশের মতো নয়। ওখান থেকে ইংরেজি বা হিন্দিতে চিঠি পাঠানো যায় না। একমাত্র উর্দুতেই ও রাজ্য থেকে চিঠি পাঠানো যায়। মণির উর্দু শেখার ব্যবস্থা আমি করেই এসেছি এবার। ওখানের এক উর্দুর অধ্যাপক আমার বহুদিনের পরিচিত। উনি এক সপ্তাহ হল মণিকে উর্দু শেখানো শুরু করেছেন। চিঠি এল বলে।
যশোদা শুনলেন। এবং বিশ্বাস করার কণামাত্র কারণও খুঁজে পেলেন না। জামাতার বহুরূপী চরিত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা হয়ে গিয়েছে ততদিনে। সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের থেকে যে ঘোর দূরবর্তী রোশনলালের অবস্থান, সেটা বুঝে গিয়েছিলেন। মুখের উপর মিথ্যেবাদী বলতে বাধে। যশোদা তাই বাক্যব্যয় করলেন না বিশেষ। রাত্রি গভীর হলে চিঠি লিখতে বসলেন ছোটভাই ভীমপ্রসাদকে। যাঁর জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল।
ভাইকে লেখা দিদির চিঠির অংশবিশেষ রইল।
স্নেহের ভীম,
আমার আশীর্বাদ নিয়ো। মণি দুই সপ্তাহ আগে রোশনলালের সঙ্গে কাশ্মীর গিয়েছিল। রোশন ন’দিন পরে ফিরে এসেছে মণিকে কাশ্মীরেই রেখে। মণি খুব অসুস্থ ছিল যাওয়ার সময়। আট মাস হয়ে গেছে গর্ভবতী। এখনও একটাও চিঠি লেখেনি। রোশন বলছে, উর্দু ভাষা ছাড়া ওখান থেকে চিঠি লেখা যায় না। আমার খুব চিন্তা হচ্ছে। তুমি একটু গণনা করে তাড়াতাড়ি জানিয়ো, মণি কী অবস্থায় আছে, কেমন আছে? ও ভাল আছে তো? আমি খুব কষ্টে আছি। দিনরাত শুধু কাঁদি। খাওয়াদাওয়া ত্যাগ করেছি। তুমি তাড়াতাড়ি জানিয়ো গণনা করে, মণি কেমন আছে। খুবই দুশ্চিন্তায় সময় কাটছে। তোমার উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।
আশীর্বাদিকা দিদি
শাক দিয়ে মাছ ঢাকারও একটা সময়সীমা থাকে। সপ্তাহে দিনদুয়েক মনোহরপুকুর রোডের ফ্ল্যাটে এসে যথাসম্ভব স্বাভাবিক আচরণ করতেন রোশনলাল। এবং যখনই আসতেন, উদ্বিগ্ন যশোদা আকুল উৎকণ্ঠায় চেপে ধরতেন জামাতাকে, ‘মণিকে নিয়ে এসো এবার? বাচ্চার জন্মের সময় তো হয়ে এল।’ সন্দিগ্ধ বেলা প্রশ্নে প্রশ্নে জেরবার করে দিতেন জামাইবাবুকে, ‘দিদি চিঠি লিখছে না কেন? দিদি ভাল আছে তো?’
রোশনলালের দুঃসহ ঠেকছিল এই অতলান্ত চাপ। যা থেকে পরিত্রাণের একটাই উপায় ছিল। সেটাই কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিলেন রোশনলাল।
১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯। বিকেল পাঁচটা নাগাদ মতিলাল নেহরু রোডের চারতলার ফ্ল্যাটে গেলেন রোশনলাল। বেলা অফিসে। সদ্য চাকরি পেয়েছেন বেঙ্গল টেলিফোনস-এ। ফিরবেন ছ’টার পরে। ফ্ল্যাটে যশোদা এবং রোশনলাল-মণির দুই সন্তান, মুন্না এবং মুন্নি। খেয়ালখুশিতে খেলছে দু’জন। যেমন খেলে রোজ।
যশোদা চা করে আনলেন রোশনলালের জন্য। ফের মণি-প্রসঙ্গ পাড়তে যাবেন, এমন সময় রোশনলাল ঝাঁপিয়ে পড়লেন শাশুড়ির উপর। গলা টিপে ধরলেন। সবলদেহী রোশনলালের বিরুদ্ধে ক্ষণস্থায়ী হল মধ্যপঞ্চাশের যশোদার যৎসামান্য প্রতিরোধ। প্রাণবায়ু নিঃশেষিত হল। মুন্না এবং মুন্নি আতঙ্কে বাক্রুদ্ধ হয়ে রইল। যশোদার দেহ ছাদে নিয়ে গেলেন রোশনলাল। মাদুরচাপা দিয়ে রাখলেন এক কোণায়। মুন্না-মুন্নিকে চকোলেট আর খেলনা দিয়ে খানিক শান্ত করে অন্য একটা ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন। এবং অপেক্ষায় থাকলেন বেলার ফেরার। যশোদার ছোটমেয়েকে বাঁচিয়ে রাখার ঝুঁকি নেওয়া চলে না।
বেলা অফিস থেকে ফিরলেন সাড়ে ছ’টা নাগাদ। অপেক্ষায় ছিলেন রোশনলাল। ঘরে ঢুকতেই ভারী হাতুড়ি দিয়ে পিছন থেকে মারলেন মাথায়। আকস্মিক আঘাতের তীব্রতায় জ্ঞান হারালেন বেলা। এরপর সংজ্ঞাহীন বেলার গলা টিপে খুন করা তো কয়েক মিনিটের ব্যাপার মাত্র। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে উপর্যুপরি দুটো খুনের পর রোশনলাল শুরু করলেন অধীত চিকিৎসাবিদ্যার নিখুঁত প্রয়োগ।
প্রস্তুতিতে কোনও ফাঁক রাখেননি রোশনলাল। নিয়ে এসেছিলেন চপার, দা, তার, দড়ি, রেশনের ঢাউস ব্যাগ, ডাক্তারির ছুরি-কাঁচি। ভেবেই রেখেছিলেন, ছাদের উপর পড়ে থাকা কাঠের পাটাতনটা ব্যবহার করবেন যথাসময়ে। করলেনও। পাটাতন নিয়ে এলেন ছাদ থেকে। রাখলেন বিছানার উপর। বেলার মৃতদেহ শুইয়ে দিলেন কাঠের উপর। ‘অপারেশন থিয়েটার’ সম্পূর্ণ।
অপারেশন থিয়েটার, না কসাইখানা? দৃশ্যপট বলবে, দ্বিতীয়টাই। কেসের কিনারা হওয়ার পরে ওই ঘরের ফরেনসিক পরীক্ষা চলাকালীন উপস্থিত ছিলেন, এমন এক পদস্থ অফিসারের ভাষায়, ‘The room bore a horrid look. It had the impression of a butcher’s shop kept uncleaned with blood and fat and pieces of flesh sticking to the floor and wall, stinking with putrid smell.’
রোশনলাল চপার দিয়ে গুঁড়োগুঁড়ো করে দিলেন বেলার হাড়। হাতে উঠে এল surgical knife। টুকরো টুকরো করে কাটলেন বেলার দেহ। দেহাংশ মুড়ে রাখলেন রেশনের ব্যাগে। তার দিয়ে বাঁধলেন ব্যাগের মুখটা। জল দিয়ে ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করলেন মেঝেতে বইতে থাকা রক্তস্রোত, যতটা সম্ভব। টুকরো হাড়, অস্থি-মজ্জা-চর্বি, মৃতার শরীর থেকে নির্গত বর্জ্য তরল.. সব মিলিয়ে ওই ঘর তখন চূড়ান্ত বিবমিষা উদ্রেককারী। কসাইখানাই!
বেলার দেহাংশ ব্যাগে ভরে মুন্না-মুন্নিকে নিয়ে রোশনলাল ঘর তালাবন্ধ করে বেরিয়ে এলেন রাত্রি দশটা নাগাদ। যশোদার লাশ পড়ে রইল ছাদে। রোশনলাল ভেবেছিলেন, আগে তো বেলার গতি করা যাক, যশোদার কাটাছেঁড়া কাল করা যাবে। তারপর ধোয়ামোছা সাফসুতরো করবেন ঘর। তালাবন্ধই থাকছে। কেউ ঢোকার নেই।
ফিরলেন কোয়ার্টারে। হাসপাতালেরই এক ইলেকট্রিক মেকানিকের জিম্মায় রাখলেন দুই শিশুকে। বললেন, ‘কিছু সমস্যা হয়েছে। ওদের মা হাসপাতালে। দিনদুয়েকের জন্য তোমার কাছে থাক।’
পাওলিনকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছিলেন রোশনলাল ১৩ তারিখ দুপুরেই, ‘Come quickly’। পাওলিন রাঁচি থেকে এসে পৌছলেন ১৫ তারিখের কাকভোরে। রোশনলাল স্টেশনে গেলেন আনতে। সঙ্গে রেশনের ব্যাগ। যাতে বেলার দেহাংশ। পাওলিনকে নিয়েই সরাসরি পৌঁছলেন দক্ষিণ কলকাতার লেকে।
আজকের লেকের যে সুসজ্জিত পরিপাটি রূপ দেখে আমি-আপনি অভ্যস্ত, সূর্যের আলো ফুটতে না ফুটতেই মর্নিং ওয়াকে আসা নারীপুরুষের যে জনস্রোত দেখে চোখ সয়ে গেছে, তেমনটা ছিল না তখন। শহরবাসী আসতেন প্রাত্যহিক, তবে কাতারে কাতারে নয়। স্বল্পসংখ্যায়। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কাঠের বেঞ্চ যা ছিল, তার সংখ্যাও খুব বেশি নয়। শান্ত সরোবর ঘিরে গাছগাছালির অবশ্য তেমন অভাব ছিল না। কোলাহলশূন্য পরিবেশ। প্রকৃতি অবকাশই পেত না পরিশ্রান্ত হওয়ার।
নির্জন জায়গা দেখে সবে ব্যাগটা ফেলতে যাবেন জলে, ত্রিলোচন নামের এক নিরাপত্তাকর্মীর নজরে পড়ে গেলেন রোশনলাল, ‘কেয়া ফেকতা হ্যায় বাবু, কেয়া ফেকতা হ্যায়?’
বিপদ বুঝে রোশনলাল দৌড়লেন ব্যাগ ফেলে। ধাওয়া করে ধরে ফেললেন নিরাপত্তাকর্মী। ব্যাগ থেকে আবিষ্কৃত হল দেহাংশ। খবর গেল টালিগঞ্জ থানায়। পুলিশ এল। রোশনলাল-পাওলিনকে নিয়ে যাওয়া হল থানায়। তারপর লালবাজারে।
একঝাঁক গোয়েন্দাদের জেরার মুখোমুখি হয়েও রোশনলাল প্রাথমিক ভাবে না ভাঙলেন, না মচকালেন। আজগুবি গপ্পো ফাঁদলেন একের পর এক। ‘খুন আমি করিনি। করেছেন পি কে কাপুর বলে এক ব্যবসায়ী, যাঁর সঙ্গে বেলার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। ঘনিষ্ঠতার ফলে বেলা গর্ভবতী হয়ে পড়েন। কাপুর নামের ভদ্রলোক বেলাকে বিয়ে করায় নারাজ ছিলেন। তিনিই খুনটা করেছেন। কাপুর আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত। ওঁর কথায় ব্যাগটা লেকের জলে ফেলতে এসেছিলাম। খুনটা আমি করিনি।’ উন্মাদেও বিশ্বাস করবে না এই গাঁজাখুরি গল্প, তবু একচুলও নড়ছিলেন না মেজর রোশনলাল।
মতিলাল নেহরু রোডের ফ্ল্যাটের ছাদ থেকে যশোদার দেহ উদ্ধারের পরেও রোশনলাল ছিলেন অবিচলিত।
—মণি কোথায়? আপনার স্ত্রী?
—আমি কী করে বলব? আমাকে বলে তো যায়নি। আমার ওর চরিত্রের ব্যাপারে বরাবরই সন্দেহ হত। অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে গেলে অবাক হব না।
ফ্ল্যাটে পাওয়া গিয়েছিল বিভিন্ন সময়ে দিদি যশোদাকে লেখা ভীমপ্রসাদের চিঠি। পুলিশ টেলিগ্রাম করে ডেকে পাঠাল ভীমপ্রসাদকে। যিনি কলকাতায় এলেন সাম্প্রতিক অতীতে দিদির লেখা চিঠিগুলি নিয়ে। যার মধ্যে একটা ..‘মণি দুই সপ্তাহ আগে রোশনলালের সঙ্গে কাশ্মীর গিয়েছিল ..’
সেই চিঠির ব্যাখ্যা যখন চাওয়া হল, রোশনলাল দেখলেন, মিথ্যাচারে লাভ নেই আর। অস্বস্তির হাসি হেসে বললেন ‘Ok gentlemen, enough of it. No more waste of time. I have murdered Moni and left her buried under the sand at Puri.’ যখন স্বীকারোক্তি দিয়েছিলেন, কৃতকর্মের জন্য লেশমাত্র অনুতাপের আভাসও খুঁজে পাননি গোয়েন্দারা। সাধে কী লিখেছি আগে, গবেষণাযোগ্য চরিত্র!
রোশনলালকে সঙ্গে নিয়ে গোয়েন্দারা পাড়ি দিলেন পুরী। বয়ান অনুযায়ী হোটেলের পাশের সেই কুয়ো থেকে উদ্ধার হল মণির স্লিপার-চুড়ি-নেকলেস, যা চিহ্নিত করলেন ভীমপ্রসাদ। বালির স্তূপের ভিতর থেকে উদ্ধার হল মণির দেহাবশেষ। হাড়গোড়ই মূলত। মণিকে নিয়ে যে ওই হোটেলে উঠেছিলেন রোশনলাল, তার সাক্ষী তো ছিলেনই হোটেলকর্মীরা। পারিপার্শ্বিক প্রমাণের আর বাকি ছিল না কিছু।
চার্জশিট জমা পড়ার পর যথানিয়মে শুরু হল বিচার। আদালতকক্ষে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সাক্ষ্যদান এবং সওয়াল-জবাবের প্রক্রিয়ায় উত্তেজনার উপাদান থাকে না সিংহভাগ ক্ষেত্রে। রোশনলালের মামলার বিচারপর্ব অবশ্য দেখা দিল ব্যতিক্রমী চেহারায়। যেমনটা আদালতে অদৃষ্টপূর্ব।
যেন নাম-কা-ওয়াস্তে নিযুক্ত হয়েছেন অভিযুক্তের তরফের আইনজীবী। যাঁর ভূমিকা বস্তুত ক্রীড়নকের। যিনি কখন কী বলবেন, কোন যুক্তির প্রতিরোধে তুলবেন কোন তর্ক, কোন সওয়ালের প্রত্যুত্তরে আশ্রয় নেবেন কোন জবাবের, সব তো ঠিক করে দিচ্ছেন অভিযুক্ত নিজেই। রোশনলাল স্বয়ং। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েই হোক বা বা কোর্ট লক-আপে বন্দি অবস্থায়। অত্যুৎসাহে কখনও কখনও আইনজীবীকে থামিয়ে দিয়ে নিজেই প্রতিপক্ষের সঙ্গে তর্ক জুড়ছেন। থামাতে হচ্ছে বিচারককে। কখনও দু’ পক্ষের যুক্তিজাল শুনতে শুনতে ভ্রুকুঞ্চিত। কখনও আবার ফেটে পড়া অট্টহাস্যে। মামলার চড়াই-উতরাইয়ে অশেষ আগ্রহী কখনও, কখনও নিরাসক্ত নিস্পৃহ। এক উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিককে আদালতে দাঁড়িয়েই কথায় কথায় বলেছিলেন, দিব্যি উপভোগ করছেন ‘… fun of a trial.’
সমাজের সর্বস্তরে প্রবল কৌতূহল উৎপন্ন হয়েছিল এই মামলার গতিপ্রকৃতি বিষয়ে। বিচার চলাকালীন রোশনলালের আচরণে সেই ঔৎসুক্য তীব্রতর হয়েছিল। বিচারের দিনগুলিতে আলিপুরের দায়রা আদালতের স্বল্পপরিসর বিচারকক্ষে পা রাখার জায়গা হত না। এজলাসে ঠাসা ভিড় থাকত আমজনতার। যাঁদের যত না কৌতূহল ছিল বাদী-বিবাদীর প্রশ্নোত্তরে, তার ঢের বেশি ঔৎসুক্য ছিল রোশনলালকে একবার চোখের দেখা দেখায়। সেই লোকটিকে দেখায়, যে অচিন্তনীয় নৃশংসতায় হত্যা করেছে স্ত্রী-শাশুড়ি-শ্যালিকাকে। এবং অন্তত বহিরঙ্গে যাঁর বিন্দুমাত্র বহিঃপ্রকাশ নেই অনুতাপ-অনুশোচনার। বরং মরিয়া প্রয়াস রয়েছে নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করার।
নিধননাট্যের খুঁটিনাটি কাটাছেঁড়ার পর রায় যেদিন ঘোষিত হল, আলিপুর কোর্টের ভিড় সেদিন কল্পনাতীত মাত্রাছাড়া। পরিস্থিতি আঁচ করে আগেভাগেই মোতায়েন বাড়তি পুলিশ। কৌতূহলী জনজোয়ার নিয়ন্ত্রণে নজিরবিহীনভাবে আদালতের বাইরের রাস্তায় ঘোড়সওয়ার পুলিশের দাপাদাপি। যানবাহনের গতি বাধ্যতই শ্লথ, সংলগ্ন রাস্তাগুলিতেও।
জুরিদের মতামতের সঙ্গে সহমত হয়ে বিচারপতি কে এন ভট্টাচার্য যখন ঘোষণা করতে চলেছেন চূড়ান্ত রায়, উত্তেজনার পারদ তখন বেহিসেবি রকমের ঊর্ধ্বমুখী। ‘Taking into consideration the facts and circumstances of the case…’ বিচারসিদ্ধান্ত পাঠ যখন শুরু হল, এজলাসে নীরবতা নিশ্ছিদ্রতম।
‘As the accused deliberately and in cold blood murdered Jashoda Sharma, Moni Sharma and Bela Sharma and as there are no extenuating circumstances, the only sentence that can be awarded to the accused in this case is death. I, therefore, sentence the accused Roshanlal to death and direct that he be hanged by the neck till he is dead…’
ফাঁসির হুকুম শোনার পর যখন জনতার সহর্ষ উল্লাস এজলাসকক্ষে, মুহূর্তের জন্য বিচলিত দেখিয়েছিল রোশনলালকে। কিন্তু ওই মুহূর্তের জন্যই। সামলে উঠে ক্ষণিক পরেই দৃপ্ত নির্দেশ দিয়েছিলেন আইনজীবীকে, ‘Let’s appeal to higher courts.’ পাওলিন দোষী সাব্যস্ত হননি। আদালতের বিচারে বেকসুর খালাস।
উচ্চতর আদালতে রোশনলাল আবেদন করেছিলেন শাস্তি হ্রাসের। কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি স্যার ট্রেভর হ্যারিস পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছিলেন সে আর্জি। বড়লাটের শরণাপন্ন হয়েছিলেন রোশনলাল। ক্ষমাভিক্ষা করেছিলেন এবং প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। ‘ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা’, সেখানে নিষ্ঠুর হতে পেরেছিলেন বড়লাট। অপরিবর্তিত থেকেছিল মৃত্যুদণ্ডাদেশ। যা কার্যকর হয়েছিল ১৯৫১ সালের ২০ অক্টোবরের উষাকালে।
হাতে গোনা কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী কারাকর্মীর বয়ান অনুযায়ী, ফাঁসিকাঠের পাটাতনে পা রাখার ঘণ্টাখানেক আগেও রোশনলাল ছিলেন শান্ত-স্থিতধী। বলেছিলেন, ‘যা করেছি, তাতে ফাঁসিই উপযুক্ত শাস্তি।’
ডক্টর জেকিল।
কিন্তু মৃত্যুমুহূর্ত যখন উপস্থিত হয়েছিল, সহসা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, ‘আমি হিন্দু। আমি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করি। আমার মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী, তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য আমি হাজারবার জন্ম নেব।’
মিস্টার হাইড।
কী হয়েছিল মুন্না-মুন্নির? রোশন-মণির দুই সন্তানের? ‘Society for the Protection of Children in India’ নামের এক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল দুই শিশুর পরিচর্যার। মুন্না এবং মুন্নি প্রত্যক্ষদর্শী ছিল দিদা যশোদাদেবীর খুনের। শক-এর তীব্রতায় বাক্শক্তি হারিয়ে ফেলেছিল মুন্না। কেউ কাছে এলেই পরিত্রাহি চিৎকার করে কাঁদত শুধু। কিছু খেতে চাইত না। ১৯৫০ সালে মারা গিয়েছিল ক্যাম্পবেল হাসপাতালে। বাঁচেনি মুন্নিও। রোগজীর্ণ অবস্থায় দাদার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল এক বছর পর।
আরও লেখাই যায়। লিপিবদ্ধ তো রয়েইছে দুই শিশুর তিলেতিলে মৃত্যুযাপনের রোজনামচা। লেখাই যায়, কীভাবে আক্ষরিক অর্থেই জীবন্মৃত হয়ে গিয়েছিল অভিভাবকহীন দুই শিশু। লেখাই যায় আরও।
থাক। মৃত্যু-রোমন্থন থাক।
‘কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে?’
২.০২ মেলাবেন তিনি মেলাবেন
[উদয় সিং হত্যা
অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়, গোয়েন্দাবিভাগের সহ নগরপাল। ২০০৪ সালে ভারত সরকারের প্রদত্ত ‘ইন্ডিয়ান পুলিশ মেডেল’-এ সম্মানিত। ২০০৯ সালে পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ‘প্রশংসা পদক’। কর্মক্ষেত্রে ধারাবাহিক প্রশংসনীয় দক্ষতার জন্য ‘রাষ্ট্রপতি পদক’ পেয়েছেন ২০১৭ সালে।]
শুধু ‘হোলি হ্যায়’ চিৎকারটাই যা বাকি!
আবির হরেক রঙের। লাল-নীল-সবুজ, বেপরোয়া উড়ছে হাওয়ায়। আলিপুর কোর্ট প্রাঙ্গণে উদ্দাম উল্লাসে ঊর্ধ্ববাহু একদঙ্গল যুবক। দুধসাদা পাজামা-পাঞ্জাবি সবার। হাতে ঠোঙা ভরতি আবিরের স্টক অফুরান। অকৃপণ ওড়াচ্ছে জয়োৎসবে। ফুর্তির উপলক্ষ? তিন যুবক, যারা নায়কোচিত ভঙ্গিতে বেরচ্ছে এজলাস থেকে।
একটু আগে রায় ঘোষণা করেছেন বিচারক। ওরা তিনজন বেকসুর খালাস পেয়েছে খুনের মামলা থেকে। বছর চারেক জেলবন্দি থাকার পর। আদালত চত্বরে ভিড় জমানো অনুরাগীরা সাদরে স্বাগত জানাচ্ছে মুক্তিপ্রাপ্ত অভিযুক্তদের। আবিরে নিমেষে রংবেরং করে দিচ্ছে একে-অন্যের সাদা পাঞ্জাবি।
অতনু দেখছিলেন স্তব্ধ হয়ে। অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়, লালবাজারের গোয়েন্দাবিভাগের হোমিসাইড শাখার তরুণ সাব-ইনস্পেকটর। জোড়া খুনের ঘটনা ঘটেছিল ’৯৭-এর ৬ ডিসেম্বর। রায় বেরল আজ, ২০০১-এর ৩০ অগস্ট। খুনের কিনারা তো ঘটনার দিনই হয়ে গিয়েছিল। মাথা খাটানোর বিশেষ ব্যাপার ছিল না। খুনটা যারা করেছিল, ধরতে খুব একটা কাঠখড় পোড়াতে হয়নি।
কিন্তু এটা কী হল? কী ভাবে সম্ভব? হোমিসাইড শাখার চার্জশিট চিরাচরিত ভাবে নিশ্ছিদ্র হয় বলেই গুরুত্বপূর্ণ খুনের মামলার ভার গোয়েন্দাবিভাগের উপর পড়ে। ডিপার্টমেন্ট ধরেই নেয়, হোমিসাইড কেসটা দেখছে মানে অভিযুক্তদের শাস্তি একশো শতাংশ নিশ্চিত। কোনও গল্পই থাকবে না সাক্ষ্যপ্রমাণের চক্রব্যূহ ভেদের।
এই কেসের ‘মেমো অফ এভিডেন্স’ আর চার্জশিটে মাছি গলার মতো ফাঁকও রাখেননি অতনু। গত রাতেও নিশ্চিত ছিলেন, চার অপরাধীর দোষী সাব্যস্ত হওয়া তো স্রেফ নিয়মরক্ষা। মৃত্যুদণ্ডের সম্ভাবনা নেই, তবে যাবজ্জীবন তো অবধারিত।
অথচ সব হিসেব উলটে গিয়ে বেকসুর খালাস! তাচ্ছিল্যের হাসি ছুড়ে দিচ্ছেন অভিযুক্তদের আইনজীবী। যাঁর শরীরী ভাষায় দিব্যি পড়া যাচ্ছে, ‘কী? কেমন দিলাম!’ ইচ্ছে করেই গা ঘেঁষে মুঠো মুঠো আবির ওড়াচ্ছে খালাস হওয়া তিন যুবকের চেলাচামুন্ডারা। উড়ে আসছে কান গরম করে দেওয়া বক্রোক্তি, ‘লালবাজার তো ফুটে ফুলকপি রে!’ বাকিরা সুর করে গলা মেলাচ্ছে সোৎসাহে, ‘ফুটে কী? ফুটে ফুলকপিইইই!’
ক্ষোভ-দুঃখ-অপমান একত্রে সঙ্গী হলে যা হয়, মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করে ছত্রিশ বছরের অতনুর। কালকের খবরের কাগজে ফলাও করে বেরবে এই রায়, ‘পুলিশি তদন্তে ফাঁক, মুক্তি পেল উদয় সিং হত্যামামলার অভিযুক্তরা, তীব্র ভর্ৎসনা তদন্তকারী অফিসারকে’ ইত্যাদি প্রভৃতি। ডিপার্টমেন্টে মুখ দেখাবেন কী করে? পরিশ্রমী এবং অনুসন্ধিৎসু স্বভাবের জন্য ওসি হোমিসাইড বিশেষ স্নেহ করেন অতনুকে। জটিল মামলা এলে খোদ ডিসি ডিডি প্রায়ই বলে থাকেন, ‘এটা অতনু করুক!’ এ যা হল, কেরিয়ারেই তো কালো দাগ পড়ে গেল!
.
দুম! দ্রাম!
প্রথমে বিকট শব্দে গোটাকয়েক বোমা। ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার চারদিক। তারপর গুলি কয়েক রাউন্ড।
ফ্ল্যাশব্যাকে ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭। সকাল দশটা। ওয়াটগঞ্জ থানা এলাকার রামকমল স্ট্রিটের লাগোয়া রকে বসেছিলেন উদয় সিং। রোজকার মতো আড্ডা দিচ্ছিলেন চায়ের কাপ হাতে। পাশে সর্বক্ষণের ছায়াসঙ্গী নরেশ, কল্যাণ, বোম্মাইয়া। উলটোদিকের ফুটপাথে নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করছিলেন উদয়ের ছোটভাই রঞ্জিত আর স্থানীয় যুবক নিতাই, যিনি উদয়ের ব্যবসায় দীর্ঘদিনের কর্মী।
হঠাৎই হাতে বোমা-পিস্তল নিয়ে আবির্ভাব চার যুবকের। সোজা উদয়ের দিকে ধেয়ে এসে বোমা-গুলির দুম-দ্রাম, নির্বিচারে। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল, বোমা নয়। একাধিক স্প্লিন্টার ঢুকল উদয় আর নরেশের শরীরে। রক্তাক্ত শরীর দুটো ঢলে পড়ল মাটিতে। অল্পের জন্য অক্ষত থাকলেন আড্ডার অন্য দুই সঙ্গী, কল্যাণ আর বোম্মাইয়া।
আতঙ্কের ঘোর কাটিয়ে উলটোদিকের ফুটপাথ থেকে যতক্ষণে রঞ্জিত-নিতাই ছুটে এসেছেন রাস্তার এপারে, গুলি ছুড়তে ছুড়তে তখন ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছে চার আততায়ী। ঘটনা যেখানে ঘটছে, সে-রাস্তা দিনভর ব্যস্ত থাকে লোকজনের আনাগোনায়। তার উপর সময়টা ভাবুন, সকাল দশটা! জনতা ধাওয়া করল ঘাতক চতুষ্টয়ের পিছনে। তিনজন পালাল নাগালের বাইরে। চতুর্থ আততায়ী পিছিয়ে পড়ল কিছুটা, পিছনে রে-রে করে ছুটে আসা দঙ্গলটার সঙ্গে কমতে থাকল ব্যবধান।
উদয় আর নরেশের রক্তে ভেসে যাওয়া শরীর দুটো যখন স্থানীয়রা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়িতে তুলছেন, ততক্ষণে আশেপাশে খবর ছড়িয়ে পড়েছে উল্কাগতিতে। উদয় সিং বোমার আঘাতে গুরুতর আহত, বেঁচে থাকার সম্ভাবনা শূন্যের কাছাকাছি। সেই উদয় সিং, যার অঙ্গুলিহেলনে চালিত হয় বন্দর এলাকার একটা বড় অংশের অন্ধকার জগৎ। স্থানীয়দের কাছে যিনি হয় ‘উদয় ভাই’, নয় ‘উদয় ভাইয়া’।
সোয়া দশটা নাগাদ ফোনে খবর এল ওয়াটগঞ্জ থানায়। উদয় সিং-এর উপর গুলিবোমার প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে এলাকায়, আন্দাজ করতে তিরিশ সেকেন্ডের বেশি লাগল না ওসি-র। প্রথম ফোনটা করলেন ডিসি পোর্টকে, দ্বিতীয়টা লালবাজার কন্ট্রোল রুমে। ডিসি রওনা হলেন রামকমল স্ট্রিটের উদ্দেশে। পোর্ট ডিভিশনের সমস্ত থানার ওসিদের ওয়ারলেস মারফত জরুরি নির্দেশ পাঠালেন ডিসি হেডকোয়ার্টার, ‘স্পটে যান।’ গার্ডেনরিচ-একবালপুর-মেটিয়াবুরুজ-নর্থ পোর্ট-ওয়েস্ট পোর্ট-সাউথ পোর্ট, সব থানার গাড়ি ছুটল। হাতের কাছে যা ফোর্স-অফিসার আছে, তাই নিয়ে। লালবাজার থেকেও তড়িঘড়ি ওয়াটগঞ্জে রওনা দিল RAF।
‘ধুন্ধুমার’ আজকাল মিডিয়ার খুব প্রিয় শব্দ। চ্যানেলে হোক বা খবরের কাগজে, দু’-চারজনের মধ্যে কোথাও সামান্য খুচরো খুনসুটির ঘটনা ঘটলেও অবলীলায় ব্যবহৃত হয় ‘ধুন্ধুমার’, পরিস্থিতি সে যতই হোক তেমন কিছুর যোজনখানেক দূরে।
থানা থেকে খুনের জায়গাটা খুব বেশি হলে পৌনে এক কিলোমিটার। পুলিশ যখন পৌঁছল, রামকমল স্ট্রিটে তখন আক্ষরিক অর্থেই ধুন্ধুমার। দোকানপাট যত ছিল রাস্তার দু’ধারে, ঝাঁপ পড়ছে দ্রুত। উদয় সিং-এর অনুগামীরা জড়ো হয়েছে শয়ে-শয়ে। হাতে লাঠি আর পাকানো বাঁশ। পথচলতি গাড়িঘোড়ায় এলোপাথাড়ি ভাঙচুরে ঘটছে ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ। পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করে ইটবৃষ্টি চলছে লাগাতার।
এ অবস্থায় যা করতে হয়, যা করা উচিত, করল পুলিশ। বেধড়ক লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস এবং ধাওয়া করে ধরপাকড়, যতজনকে পারা যায়। প্রায় ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় যখন পরিস্থিতি কিছুটা আয়ত্তে এল, ফের শুরু হল যানচলাচল, খবর এল ক্যালকাটা হসপিটাল (বর্তমানের সিএমআরআই) থেকে। উদয় সিং মৃত। নরেশ লড়ছেন, তবে সে লড়াইয়ে হার প্রায় নিশ্চিত। ডাক্তাররা জানিয়েই দিয়েছেন একরকম, আর কয়েক ঘণ্টা বড়জোর।
.
ওয়াটগঞ্জ থানা, কেস নম্বর ২৭৫, তারিখ ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭। ধারা, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩০৭/৪২৭/৩৪, খুন, খুনের চেষ্টা, সম্পত্তির ক্ষতি এবং একই অপরাধের উদ্দেশ্যে একাধিকের সম্মিলিত পরিকল্পনা,
২৫ (১বি)(A)/২৭ অস্ত্র আইন, ৩ এবং ৫ বিস্ফোরক পদার্থ আইন।
দুষ্কৃতীদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের পরিণতিতে গুলি, বোমাবাজি এবং খুন। ঘটনা আজ থেকে একুশ বছর আগের। এবং একেবারেই অভূতপূর্ব নয়। দুষ্কৃতীদের এলাকা দখলের লড়াইয়ে এমন ঘটনা এর আগেও ঘটেছে। পরেও। উপরন্তু এ মামলাতে প্রথাগত রহস্য নেই, কিনারাপর্বে নেই মস্তিষ্কের কসরত।
তবু এ কাহিনি বহু আলোচিত কলকাতা পুলিশের ইতিহাসে। তথাকথিত ‘ওপেন অ্যান্ড শাট’ মামলাও যে কী গভীর বিড়ম্বনায় কখনও কখনও ফেলে দিতে পারে বাস্তবের গোয়েন্দাদের, কী দুঃসহ পরীক্ষা যে নেয় ধৈর্যের-স্থৈর্যের-মনোবলের, আলোচ্য কেসের ইতিবৃত্ত তার প্রামাণ্য দলিল।
ঘটনায় ফিরি। যেমন ভাবা গিয়েছিল, উদয়ের সঙ্গী হলেন আহত নরেশও। মারা গেলেন বিকেল সোয়া চারটে নাগাদ। ময়নাতদন্তে নতুন কিছু পাওয়ার ছিল না। রুটিন কাটাছেঁড়ার পর রুটিন রিপোর্ট, শরীরের বিভিন্ন অংশে স্প্লিনটারের আঘাতে মৃত্যু।
মারমুখী জনতাকে হঠিয়ে দিয়ে যখন এলাকার দখল নিয়েছে পুলিশ, খবর এল, কাছেই মণিময় ব্যানার্জি রোডে গুরুতর জখম অবস্থায় পড়ে আছে এক যুবক। ওসি ছুটলেন।
ড্রেনের ধারে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা যুবকের শার্ট রক্তে মাখামাখি। পাশে একটা দেশি রিভলভার পড়ে আছে। তুলে দেখা গেল, সেমি-লোডেড। চেম্বারে এখনও তিন রাউন্ড গুলি। স্থানীয় মানুষ এসব ক্ষেত্রে এতটাই ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন, মুখ খুলতেই চান না কেউ। যাকেই জিজ্ঞেস করা হোক, কাটা রেকর্ডের মতো বাজতে থাকে, ‘আমি তো কিছু দেখিনি সেভাবে।’ স্বাভাবিকই। কে আর চায় খামোখা খুনখারাপির মামলায় জড়াতে? কিছু বললেই পুলিশ বয়ান নেবে। তাতে সইসাবুদ করতে হবে। কোর্টে ডাক পড়বে সাক্ষী দিতে। কী লাভ অত ঝামেলায় গিয়ে? এমনি এমনি কি আর বলে, ‘পুলিশে ছুঁলে…!’
কথাবার্তা বলে তবু জানা গেল যতটুকু, এই আহত যুবককে ধাওয়া করেছিল জনা কুড়ি-পঁচিশের একটা দল। হাতে রিভলভার উঁচিয়ে পালাচ্ছিল যুবক। একটা সময় আর পেরে ওঠেনি দৌড়ে। ধরে ফেলেছিল পিছু-নেওয়া জনতা। কিল-ঘুষি-লাথি কিছুক্ষণ চলেছিল যা খুশি, যেমন খুশি। কৌতূহলী স্থানীয় মানুষের ভিড় বাড়তে থাকলে ওই অবস্থায় যুবককে ফেলে রেখে উধাও হয়ে যায় ওই কুড়ি-পঁচিশ।
রক্তপাত হয়েছে প্রচুর। তবে যুবক তখনও বেঁচে। গাড়িতে করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। তবে তার আগেই জানা হয়ে গেছে পরিচয়। ওসি একঝলক দেখেই চিনেছিলেন। এর নাম বাদল। বাদল মুখার্জি। বেহালার পাঠকপাড়ায় বাড়ি। খিদিরপুর এলাকায় একটা দোকান আছে। আগে একাধিকবার ধরা পড়েছে তোলাবাজি-মারদাঙ্গার অভিযোগে। উদয়ের বিরোধী গোষ্ঠীর মস্তানদের মধ্যে এই বাদল বরাবরই প্রথম সারিতে। নির্ঘাত উদয়কে যারা মারতে এসেছিল, তাদের মধ্যে ছিল। পালাতে পারেনি, মার খেয়েছে বেধড়ক। মরেই যেত আর একটু হলে। অবশ্য চোট-আঘাতের যা অবস্থা, মরে যে যাবে না, গ্যারান্টি নেই কোনও।
বাদল পালাতে পারেনি। কিন্তু যারা পেরেছে, তারা কারা? কোথায় পালাল? এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া নিয়ে চিন্তিত দেখাচ্ছিল না ওসি-কে। দিনের আলোয় মেরেছে। পালানোর সময় একজন গণপিটুনিতে হাসপাতালে। অন্যদের নাম জানা যাবে দ্রুতই। এবং জানার পর গ্রেফতার তো স্রেফ সময়েরই ব্যাপার। গ্যাং-ওয়ারের ঘটনায় যেমন হয়।
খুনিরা পালিয়ে যাবেই বা কোথায়? আর গেলেই বা কতদিন? এখন ঢের বেশি জরুরি এলাকার আইনশৃঙ্খলার স্থিতাবস্থা, ফের যাতে গোলমাল না বাধে, সেটা নিশ্চিত করা। কোথায় কোথায় পুলিশ পিকেট বসবে আগামী সাতদিন, টহলদারি গাড়ি কোথায় কোথায় নজর রাখবে বেশি, ওসি তৈরি করতে শুরু করলেন ব্লু প্রিন্ট। থানার এত কাছে গুলি-বোমা-খুন, এমনিতেই লজ্জার। ফের একটা কিছু ঘটে গেলে চাকরি নিয়েই টানাটানি হওয়ার সম্ভাবনা।
এ মামলা ডিডি নেবে, জানাই ছিল। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের সাব-ইনস্পেকটর অতনু বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেকে গোয়েন্দাপ্রধান জানিয়ে দিলেন, ‘কেসটা তুমি করছ। ডিটেকশন তো হয়েই গেছে ধরে নাও। অ্যারেস্টগুলো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করার চেষ্টা করো। অতনু, আই ওয়ান্ট আ কুইক চার্জশিট, অ্যান্ড কনভিকশন অ্যাট এনি কস্ট।’
—রাইট স্যার।
অতনু মাথা নেড়ে বেরিয়ে আসেন ঘর থেকে। আপাতত প্রথম কাজ, উদয় সিং-এর ঠিকুজিকুষ্ঠি একটু ঝালিয়ে নেওয়া। অপরাধজগতের পরিচিত নাম, গুন্ডাদমন শাখায় খুঁজলেই পুরনো রেকর্ড পাওয়া যাবে নিশ্চিত।
.
উদয় সিং। তিন ভাইয়ের মধ্যে মেজো। সংগ্রাম-উদয়-রঞ্জিত, তিন ছেলেকে নিয়ে বছর পঁচিশ আগে বাবা ছোটু সিং উত্তরপ্রদেশ থেকে কলকাতায় চলে এসেছিলেন জীবিকার খোঁজে। ছোটু কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টে কাজ জুটিয়ে নিয়েছিলেন ঠিকাশ্রমিকের।
তিন ছেলেকে ভরতি করে দিয়েছিলেন স্কুলে। সংগ্রামের পড়াশুনো বেশিদূর এগোয়নি। রঞ্জিত তুলনায় বেশি মনোযোগী ছিল লেখাপড়ায়। উদয়ের অবশ্য তীব্র বিরাগ ছিল বইখাতার প্রতি। পাড়া-বেপাড়ায় ফুটবল খেলে বেড়ানো, সন্ধেবেলায় গঙ্গার পাড়ে বসে বিড়ি-সিগারেট-চোলাই আর পয়সাকড়ি জুটিয়ে এলাকার সিনেমা হলে নুন শো-য় অ্যাডাল্ট ফিলমের আঁচ পোহানো, মোটামুটি এই ছিল উদয়ের কিশোরবেলা।
বড়ছেলে সংগ্রামের বয়স যখন বছর কুড়ি-বাইশ, পরিচিত একজনকে বলেকয়ে ফ্যান্সি
মার্কেটের একটা দোকানে হেল্পারের কাজে লাগিয়ে দিলেন ছোটু সিং। বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিছু তো কাজকর্ম করুক। সে মাইনে যত কমই হোক। সংগ্রাম ক্রমশ টাকা জমিয়ে বছরকয়েকের মধ্যে ফ্যান্সি মার্কেটে একটা দোকান চালু করলেন। নিজের মতো থাকতেন। ভাইদের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল না বিশেষ।
উদয়ের জন্যও ছোটু সিং কাজ দেখলেন গুলমোহর ঘাটের ফুলপট্টিতে। সাপ্লাই যখন আসবে, ট্রাক থেকে দোকানে মাল নামানোর কাজ। উদয় কাজে গেল সুবোধ বালকের মতো। সন্ধেবেলা বাড়ি বয়ে এসে মালিক জানিয়ে দিয়ে গেল ছোটু সিং-কে, ‘কাল থেকে ওর আর আসার দরকার নেই। পাঠাবেন না।’
—কেন?
—আপনার ছেলে অত্যন্ত বেয়াদব। ফুলের ডালা নামানোর সময় ট্রাকের হেল্পারের সঙ্গে সামান্য কারণে তর্ক করেছে। মা-বাবা তুলে যা-তা গালাগালি দিয়েছে। হেল্পারের গায়েও হাত তুলেছে। ওকে আমি কাজে রাখব না।
ছোটু সিং বিস্তর বকাঝকা করলেন উদয়কে। যে বিন্দুমাত্র বিচলিত হল না বাবার গালমন্দে। আঠারো বছরের উদয় ততদিনে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে, এসব দু’পয়সার খালাসির কাজ তার জন্য নয়। কে খাটবে এত ফাইফরমাশ? অনেক বড় মাঠ পড়ে আছে তার খেলার জন্য। খেলার নিয়মগুলো শুধু ভাল করে জেনে নিতে হবে।
‘বড় মাঠ’ বলতে কলকাতা বন্দর। ‘খেলা’ বলতে লোহার ছাঁটের নিলাম। ‘নিয়ম’ বলতে সিন্ডিকেটের প্যাঁচপয়জার। না ছিল পড়াশুনোর বালাই, না ছিল কাজকর্ম কোনও। হাতে যে অঢেল সময় থাকত, তার অনেকটাই উদয় কাটাত ডক-এলাকায়। দেখত অবাক হয়ে, লোহার ছাঁট নিলামের দিনের সপ্তাহখানেক আগে থেকে কীভাবে রাতারাতি বদলে যেত জাহাজের আসা-যাওয়া আর রুটিনমাফিক মাল খালাসের রোজকার শান্ত ছবিটা। এলাকায় টেনশনের গন্ধ পেতে ঘ্রাণশক্তি প্রখর হওয়ার প্রয়োজন পড়ত না।
গলায় চেন, হাতে বালা, শরীরে উল্কি, চোখে রোদচশমা। ষন্ডামার্কা চেহারার যুবকদের বাইক-সফর যেন হঠাৎই বেড়ে যেত এলাকায়, লক্ষ করত উদয়। কখনও আসলাম ভাইয়ের ছেলেরা এলাকা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, কখনও জিতেন্দর ভাইয়ের লোকজনকে বাইক নিয়ে দেখা যাচ্ছে যত্রতত্র। বাইক-আরোহীদের কোমরের কাছে যেটা উঁচু হয়ে আছে, সেটা কী, বুঝতে বুদ্ধি খরচ করতে হত না। মেশিন!
যত এগিয়ে আসত নিলামের দিন, রাত বাড়লেই ইতিউতি আওয়াজ পাওয়া যেত বোমাবাজির। গুলিরও। নিলামের পরদিন সব শান্ত হয়ে যেত ভোজবাজির মতো। বন্দর এলাকার প্রতিটা গলিঘুঁজি চেনা হয়ে-যাওয়া উদয় দেখত, কোনও না কোনও জায়গায় মোচ্ছব চলছে যুদ্ধজয়ের। বিদেশি মদের ফোয়ারা ছুটছে। উড়ে যাচ্ছে দেদার মুরগি-মটন। ঝাঁ-চকচকে গাড়ি এসে রাতের দিকে থামছে ঠেকের সামনে। ‘ভাই’-দের গাড়ি। কখনও সে ‘ভাই’-এর নাম আসলাম, কখনও জিতেন্দর, কখনও আনোয়ার, কখনও-বা রামাধীর। আসর জমে উঠছে ফের, সুর আর সুরায়। রাত গভীর হলে হুশ করে বেরিয়ে যাচ্ছে গাড়ি, ভ্রুমমম শব্দে স্টার্ট নিয়ে ছুটছে বাইকের সারি। কোথায় যাচ্ছে ওরা এত রাতে? কানাঘুষোয় শুনত উদয়, গন্তব্য নাকি সোনাগাছি। যেখানে রাত যত বাড়ে, তত নাকি রঙিন হয় দুনিয়া। সুন্দরীদের মেহফিল বসে।
বাড়ি ফিরতে ফিরতে উদয় ভাবত, আহ, এই তো জীবন। জিন্দগি হো তো অ্যায়সা!
সিনেমায় যা দেখে থাকি আমরা সচরাচর, এরপর অন্ধকার জগতের মোহে আচ্ছন্ন এই জাতীয় ছেলেরা নজরে পড়ে যায় কোনও এক ‘ডন’-এর, কোনও এক ‘ভাই’-এর। তারপর ক্রমশ নিজের যোগ্যতায় ‘ভাই’-এর বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠা। দায়িত্ব আর ক্ষমতা, দুইয়েরই পরিধি স্বাভাবিক নিয়মে বাড়তে থাকা। এবং একটা পর্যায়ের পর উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিজেই ‘ভাই’ হয়ে ওঠার, তৈরি করে ফেলা নিজস্ব অনুগামীদের বলয়। যার ছত্রছায়ায় বড় হয়ে ওঠা, তাকেই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া।
তারপর মাৎস্যন্যায়। ছোট মাছ যে ‘বড়’ হয়ে গেছে, সেটা বড় মাছ যতক্ষণে বুঝতে পারে, ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে বেশ খানিকটা। শুরু হয়ে গেছে সেয়ানে সেয়ানে টক্কর। যেখানে দয়ামায়ার জায়গা নেই, নেই নীতিনিয়মের বালাই। আছে শুধু ‘জোর যার, মুল্লুক তার’-এর আপ্তবাক্য। রামগোপাল বর্মার ‘কোম্পানি’ সিনেমার সেই গানটাই এ দুনিয়ার রিংটোন, ‘সব গন্দা হ্যায় পর ধান্দা হ্যায় ইয়ে’।
সিনেমা এক, আর বাস্তব আরেক। তবে এটা স্বীকার্য, ফিলমের প্রয়োজনে আমদানি করা নাটকীয়তার উপাদানগুলো বাদ দিলে বাস্তবের উদয়দের উত্থানের চিত্রনাট্যও মোটামুটি একই রাস্তা ধরে পথ হাঁটে। পুলিশ রেকর্ডস ঘেঁটে উদয়ের কোনও ‘গডফাদার’-এর খোঁজ অতনু পেলেন না বটে, কিন্তু একটা রেখচিত্র পাওয়া গেল আটের দশকের মাঝামাঝি থেকে বন্দর এলাকার অপরাধজগতে উদয়ের উল্কাসদৃশ উত্থানের।
গার্ডেনরিচ এলাকায় তুমুল মারদাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ে বাইশ বছর বয়সে প্রথম হাজতদর্শন। বছরখানেকের মধ্যেই দোলের দিন ক্লাবে-ক্লাবে মারামারি আর বোমাবাজিতে নেতৃত্ব দিয়ে ফের শ্রীঘরে কিছুদিন। জামিন পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টের এক শ্রমিকনেতাকে ভরদুপুরে গুলি করে খুনের চেষ্টা। চেষ্টা নয়, সরাসরি খুনই এর বছরখানেক পরে। দেড় বছর হাজতবাসের পর জামিনে মুক্তি, প্রভাব খাটিয়ে মামলাকে সময়ের হিমঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া। ক্রমে ঢুকে পড়া লোহার ছাঁটের সিন্ডিকেটে, বাহুবলে কায়েম করা দাদাগিরি, হু হু করে সংখ্যা বেড়ে যাওয়া অনুগামীর, এবং উদয় সিং থেকে ‘উদয় ভাই’ হয়ে ওঠা। হিন্দি ছবির ভাষায়, এলাকার ‘বেতাজ বাদশা’।
লম্বায় প্রায় ছ’ফুট। পাথরে কোঁদা শরীর। চওড়া কপাল, ঝাঁকড়ানো চুল। বারো মাস তিনশো পঁয়ষট্টি দিন একই পোশাক। ধবধবে সাদা শার্ট-প্যান্ট। এক কথায়, নায়কোচিত চেহারা ছিল উদয়ের। আর ছিল পোর্ট ডিভিশনের নিম্নমধ্যবিত্ত এলাকায় ‘রবিনহুড’ ইমেজ। মেয়ের বিয়ের টাকা জোগাড় হচ্ছে না, দরিদ্র পিতা শরণাপন্ন হতেন ‘উদয় বেটা’-র। সম্পন্ন বাড়িওয়ালা মস্তান লাগিয়ে উচ্ছেদের হুমকি দিচ্ছে, নিরীহ ভাড়াটিয়ার মুশকিল আসান বলতে তখন ‘উদয় ভাইয়া’। পুজোর বিচিত্রানুষ্ঠানে বোম্বের শিল্পী আনার টাকা জোগাড় হচ্ছে না, ভরসার ঠিকানা সেই ‘উদয় ভাই’। যে দু’-চারটে ফোন করলেই স্থানীয় শিল্পপতিরা টাকার থলি নিয়ে হাজির। এবং পুজোয় দেদার নাচাগানা, ব্র্যাকেটে বোম্বে-মার্কা শিল্পীদের উপস্থিতিতে। জনপ্রিয়তায় বন্দর মহল্লায় একজনই প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল উদয়ের। উদয় নিজে।
একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের পর পুলিশ এবং আইনকে এড়াতে উদয়দের মতো লোকের প্রয়োজন পড়েই সামাজিক আব্রুর। সে আব্রু কখনও সরবরাহ করে থাকে ব্যবসাদারের পরিচিতি, কখনও-বা রাজনীতিকের মোড়ক। উদয় প্রথমটা বেছেছিলেন। বাড়ি কিনেছিলেন ১/১ রামকমল স্ট্রিটে। পাশেই আরেকটি দোতলা বাড়ির উপরটা ভাড়া নিয়ে ব্যবসায়িক সংস্থার অফিস খুলেছিলেন। নাম ‘বিকি এন্টারপ্রাইজ’। রঞ্জিতের অফিসও ওখানেই ছিল, ‘মা তারা এন্টারপ্রাইজ’। রঞ্জিত ঝুটঝামেলায় থাকা পছন্দ করতেন না। সোজা পথে ব্যবসা করতেন।
উদয়ের ব্যবসা ইমারতির। বাড়ি তৈরির মালমশলা সাপ্লাইয়ের। সকাল দশটায় রোজ অফিস খোলে, ঝাঁপ পড়ে যায় সন্ধে সাতটা নাগাদ। উদয়কে অষ্টপ্রহর ঘিরে থাকে নরেশ-কল্যাণ-বোম্মাইয়ারা। দিনভর লেগে থাকে লোকের ভিড়। সবাই জানে অলিখিত নিয়মটা, এলাকায় বাড়ি তৈরি করতে গেলে ইট-বালি-সিমেন্ট উদয়দের থেকেই নিতে হবে। যার ঘাড়ে মাথা থাকবে না নেওয়ার, তার বাড়িই উঠবে না। বাংলা হিসেব।
ফুলেফেঁপে উঠেছিলেন উদয়। লোহার ছাঁটের নিলামেও কায়েম রেখেছিলেন একাধিপত্য। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের থেকে তোলাবাজির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তো ছিলই। কারও সাহস ছিল না পুলিশে অভিযোগ করার। পুলিশের কিছু আইনত করারও ছিল না উদয়ের ব্যাপারে, যতক্ষণ না জমা পড়ছে লিখিত অভিযোগ, যতক্ষণ না উদয় নতুন করে সরাসরি জড়াচ্ছেন মারদাঙ্গায়। উদয় বুদ্ধিমান ছিলেন। ব্যবসার আড়ালেই সব কিছু যখন নির্বিঘ্নে চলছে রক্তপাতহীন, ভালই তো! গত তিন-চার বছরে সবরকম ঝামেলার থেকে নিজেকে দূরে রেখেছিলেন।
স্ত্রী সমর্থন করতেন না উদয়ের কাজকর্ম। তিতিবিরক্ত হয়ে একটা সময় একমাত্র সন্তানকে নিয়ে উঠে গিয়েছিলেন হাজরার কাছে বাপের বাড়িতে। পরিবার আর ব্যবসা সমার্থক হয়ে গিয়েছিল ঝাড়া হাত-পা উদয়ের কাছে।
তবে ওই যে, ‘চিরদিন কাহারো সমান নাহি যায়’। উদয় গত সাত-আট মাস ধরেই খবর পাচ্ছিলেন, এক তরুণ তুর্কির উদয় হয়েছে এলাকায়। ধমকে-চমকে যে তোলাবাজি চালাচ্ছে সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে। একদিন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা দল বেঁধে অভিযোগ জানিয়ে গেলেন উদয়ের দরবারে, ‘ভাইয়া, একটু দেখুন। আমরা তো টিকতে পারছি না অত্যাচারে।’ উদয় নড়েচড়ে বসলেন একটু। বোম্বাইয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কী নাম রে ছেলেটার? খোঁজখবর নিস তো একটু।’
—নিয়েছি ভাইয়া।
—নামটা কী?
—বামা।
—বামা?
.
অতনুর প্রশ্নের উত্তরে এক মুহূর্তের জন্যও ভাবতে হয় না খুনের প্রত্যক্ষদর্শী রঞ্জিত-গোপাল-কল্যাণ-বোম্বাইয়াদের।
—স্যার, বামার ছেলেরা মেরেছে। বামা, বাদল, পটা আর টুটি, চারজনকে স্পষ্ট দেখেছি। এল, আর বোম মারতে শুরু করল ভাইয়াকে লক্ষ্য করে। গুলিও চালাল।
বামা, পটা, টুটি। এদের আসল নাম জানতে চেয়ে লাভ নেই। অতনু বোঝেন, বলতে পারবে না এরা। জেনে নিতে হবে থানার রেকর্ড থেকে, নিশ্চয়ই দু’-চারবার ধরা পড়েছে আগে। তা ছাড়া মস্তানদের তো এরকমই নাম হয়। মা-বাবার দেওয়া ভাল নামটা নিজেরাই ভুলে যায় এরা একটা সময়। নাম হয়তো গোপালচন্দ্র অমুক। পরোটা ভেজে বিক্রি করত। কোনও একটা ঝামেলায় পরোটা ভাজার তাওয়া দিয়েই মাথায় মেরে খুন করেছিল কাউকে। সেই থেকে নাম ‘পরোটা গোপাল’। কিংবা ধরুন, নাম ছিল হরেন্দ্রনাথ তমুক। বোম বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণে একটা চোখ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অনিবার্য নামকরণ, হাফচোখো হরেন। কিংবা কোনও না কোনও বিচিত্র সংযোগে কারও না কারও নাম ‘বোম বিশু’, ‘ত্যাবড়া তপন’, ‘উল্লু রাজু’। অথবা, গালকাটা গদাই, কানকাটা কানাই, বা হাতকাটা দিলীপ।
থানার নথিপত্র থেকে জানা গেল ভাল নামগুলো। প্রণব নাগ ওরফে বামা, খিদিরপুর এলাকারই হরিসভা লেনের বাসিন্দা। শংকরসুন্দর দত্ত ওরফে টুটি, বাড়ি খিদিরপুরেই। শুভাশিস মুখার্জি ওরফে পটা, স্থানীয় যুবক।
বাদল চিকিৎসাধীন এসএসকেএম-এ। পটা-টুটি-বামা, তিনজনের বাড়িতেই রেইড করা হল। জানাই ছিল, থাকবে না কেউ। পাওয়া গেল না। সোর্স লাগানো হল একাধিক। এলাকার বিভিন্ন ঠেকে সাদা পোশাকে নজরদারি শুরু করলেন গুন্ডাদমন শাখার অফিসাররা। তিনজনই স্থানীয় মস্তান। যত দাদাগিরি, এলাকাতেই। আজ নয় তো কাল, পরশু নয় তরশু, ফিরবেই মহল্লায়। যাবে কোথায়?
যা ভাবা গিয়েছিল, তাই। টুটি এবং পটা ধরা পড়ল ঘটনার দিন পনেরো পর, ২২ ডিসেম্বর। হাওয়া এখনও কতটা গরম, সেটা বুঝতে গভীর রাতে দু’জনে ঢুকেছিল গার্ডেনরিচ এলাকায়। গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং-এর পিছনে এক গোপন ডেরায় মদের বোতল খুলে বসার আধঘণ্টার মধ্যে খবর চলে এসেছিল সোর্স মারফত। যে রিভলভার দিয়ে পটা গুলি চালিয়েছিল খুনের দিন, সেটা উদ্ধার হল। নিজের বাড়ির কাছেই একটা পুকুরের ধারে পুঁতে রেখেছিল। বাকি ছিল প্রণব ওরফে বামা। জালে উঠল মাঝেরহাট এলাকা থেকে, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই। ’৯৮-এর জানুয়ারি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়া মাত্রই হেফাজতে নেওয়া হল বাদলকে। সম্পন্ন হল গ্রেফতারি-পর্ব।
খুনের কারণ? জেরায় জানা গেল, বামার নেতৃত্বে পটা-টুটি-বাদল এবং আরও বেশ কয়েকজন যুবক বছরখানেক হল নিজেদের ‘গ্যাং’ তৈরি করেছিল। যে ‘গ্যাং’-এর মূল উদ্দেশ্যই ছিল, উদয়ের একচ্ছত্র রাজ্যপাটে ভাগ বসানো। মাসছয়েক আগে পোর্টের মালপত্র সরবরাহের একটা বড় অঙ্কের টেন্ডার হয়। এসব টেন্ডারে উদয়ের অর্ডার পাওয়াটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল এতদিন। নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়েছিল বামা-বাহিনী। তারাও টেন্ডার ফর্ম তুলেছিল, সমানে-সমানে লড়েছিল। অর্ডার শেষ পর্যন্ত উদয়ের টিমই পেয়েছিল, কিন্তু গোকুলে যে প্রতিদ্বন্দ্বীরা বেড়ে উঠছে, সে ইঙ্গিত পেয়ে গিয়েছিলেন ‘উদয় ভাইয়া’। সে-রাতেই উদয় স্বয়ং দলবল নিয়ে বামার বাড়ি গিয়ে শাসিয়ে এসেছিলেন, ‘এই দুঃসাহস যেন আর না হয়!’
ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, আরও ঘোরতর দুঃসাহস দেখিয়েছিল পটা-টুটি-বাদলরা। পরদিন বিকেলে, উদয় তখন অফিসে অনুপস্থিত, সদলবলে হানা দিয়েছিল রামকমল স্ট্রিটে। অফিসে যারা ছিল, তাদের সামনে পিস্তল উঁচিয়ে হুমকি দিয়েছিল, ‘ভাইয়াকে বলে দিস, সে জমানা আর নেই। তোরা থাকলে আমরাও থাকব। কে কবে মাছের চারা ছাড়বে, তার ভরসায় পুকুর কাটব না, বলে দিস।’
এ হুমকির পালটা প্রত্যাঘাত কেন উদয় করেননি, শক্তির বিচারে এগিয়ে থাকা সত্ত্বেও, আন্দাজ করতে পেরেছিলেন অতনু। মারপিট-খুনজখমে জড়িয়ে ফের পুলিশি ঝামেলায় পড়তে চাননি। লোক লাগিয়ে শায়েস্তা করতে পারতেন বামাদের, ইচ্ছে করলেই। করেননি, কারণ, জানতেন, শেষ পর্যন্ত নাম জড়াবেই। অন্য চাল চেলেছিলেন। নিজে থানায় গিয়ে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়ে এসেছিলেন পটাদের নামে। যে খবর আরও খেপিয়ে তুলেছিল বামা-পটার দলবলকে।
চাপা টেনশন একটা ছিলই। যা তুঙ্গে উঠেছিল দিনদশেক আগে। উপলক্ষ, আরেকটা টেন্ডার। দু’পক্ষই ফর্ম জমা দিয়েছিল। কিন্তু বামা-পটা খবর পেয়েছিল, উদয় পোর্ট ট্রাস্টের উপরমহলে কলকাঠি নেড়েছেন। যার ফলে বামাদের জমা দেওয়া ফর্ম বাতিল হতে চলেছে টেকনিক্যাল কারণ দেখিয়ে। ফের বামা-পটা-টুটি-বাদল সটান উদয়ের অফিসে গিয়েছিল। এবারও এমন একটা সময়ে, যখন উদয় অফিসের বাইরে। অ্যাকাউন্ট্যান্টের কপালে রিভলভার ঠেকিয়ে বামা ঠান্ডা গলায় বলেছিল, ‘আমাদের টেন্ডার যদি বাতিল হয়ে যায়, তোর ভাইয়াকেও পেতে দেব না। পরেরবার যখন আসব, চেম্বার খালি করে দিয়ে যাব, মনে রাখিস।’
উদয় শুনেছিলেন সব, খুব গুরুত্ব দেননি। ভেবেছিলেন, রক্ত গরম, তাই ছেলেগুলো একটু বেড়ে খেলছে। থানায় ফের ডায়েরি করিয়েছিলেন নিতাইকে দিয়ে। পুলিশ রেইড করেছিল বামার গ্রুপের প্রত্যেকের বাড়িতে। পায়নি কাউকেই। সেই রেইডের সাতদিনের পরই দুঃসাহসিক উদয়-হত্যা।
অক্লান্ত পরিশ্রমে তিন মাসের মধ্যেই চার্জশিট পেশ করেছিলেন অতনু। রঞ্জিত-নিতাই-কল্যাণ-বোম্মাইয়া প্রত্যক্ষদর্শী ছিল খুনের। ঘটনাস্থলের পাশেই ছিল দক্ষিণ ভারতীয় খাবারের একটা দোকান। সেই দোকানের কর্মী বাচ্চুও দেখেছিল ঘটনাটা। ঘটনাস্থলের কাছেই আগ্নেয়াস্ত্র সহ বাদলের গণপিটুনিতে আহত হওয়ার প্রমাণ তো ছিলই।
উদয়ের সঙ্গে অভিযুক্তদের পুরনো শত্রুতা এবং অফিসে এসে হুমকির উল্লেখ ছিল চার্জশিটে, মোটিভ এবং পারিপার্শ্বিক প্রমাণ হিসেবে। অনেক জটিল খুনের মামলার তদন্তের অভিজ্ঞতা ছিল অতনুর। সে তুলনায় এটা ছিল ঢের বেশি সরল, সোজাসাপটা। চার্জশিট জমা দেওয়ার সময় ভেবেছিলেন, কনভিকশন নিশ্চিত। ভুল ভেবেছিলেন।
তদন্তপ্রক্রিয়া একটা বৃত্তের মতো। যে বৃত্তের তিনটে অংশ। প্রথম, ঘটে যাওয়া অপরাধ। দ্বিতীয়, অপরাধটা কীভাবে ঘটল, কেন ঘটল, কে ঘটাল, তার অনুসন্ধান। এবং অপরাধীকে চিহ্নিত করা। লিখলাম বটে ‘অপরাধী’, আসলে তো অভিযুক্ত। যতক্ষণ না আদালতের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হচ্ছে ধৃত, অভিযুক্তের গায়ে তকমা লাগানো যায় না অপরাধীর। এখানেই বৃত্তের তৃতীয় অংশের প্রবেশ। সাক্ষ্যপ্রমাণ একত্রিত করে পেশ করা চার্জশিট। এবং বিচারপর্বের চাপানউতোর।
আদ্যন্ত রসকষহীন এই তৃতীয় অংশটা। তদন্তপর্বে পুলিশের কাছে বয়ান দেওয়ার সময় যে যা বলেছিলেন, বিচারপর্বে তার অর্ধেকের বেশি সাধারণত মনেই থাকে না সাক্ষীর। কারণ, পুলিশকে বয়ান আর আদালতে সাক্ষ্যদানের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকে অনেক। দু’-তিন বছর গড়িয়ে যায় কখনও কখনও, কখনও তার ঢের বেশি। বিচারের সময় যখন দিন ধার্য হয় কোনও সাক্ষীর সাক্ষ্যদানের, তদন্তকারীকে খেয়াল রাখতে হয়, দুই বয়ান যেন মিলে যায় হুবহু, অসংগতি যেন না থাকে। মনে করিয়ে দিতে হয়, ‘তখন আমাদের এই বলেছিলেন।’ আগাগোড়াই যোগাযোগ রাখতে হয় সাক্ষীদের সঙ্গে। সে যে যেখানেই থাকুন।
আরও ঝক্কি আছে হাজার। চার্জশিট জমা করার সময় যে সাক্ষীদের সত্যনিষ্ঠ মনে হয়, তাদেরই কেউ কেউ বিচারপর্বে উলটো গাইতে শুরু করে, প্রভাবিত হয়ে পড়ে তদন্ত আর বিচারের মধ্যবর্তী সময়ে। এমনও দেখেছি আমরা, চার্জশিট দেওয়া আর সাক্ষ্যদান শুরু হওয়ার মধ্যে মূল সাক্ষীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে প্রধান অভিযুক্তের বোনের। এখন সাক্ষী যে শ্যালকের বিরুদ্ধে বিরূপ সাক্ষ্য দেবে না, জানা কথাই।
গোদের উপর বিষফোড়া হয়ে দেখা দেয় পদ্ধতিগত বিলম্ব। যে ডাক্তার কলকাতায় পোস্টমর্টেম করেছিলেন ঘটনার পর, তিনি হয়তো মাঝের বছরগুলোয় বদলি হয়ে গেছেন প্রত্যন্ত কোনও জেলায়, আসতে পারলেন না সাক্ষ্যদানের নির্দিষ্ট দিনে। পরের দিন ধার্য হল মাসদুয়েক পরে। আর, জটিল মামলায় সাক্ষীর সংখ্যা তো থাকে ন্যূনতম পঞ্চাশ-ষাট। প্রত্যেকের সাক্ষ্য, বাদী-বিবাদী পক্ষের উকিলের জেরা… সময় লাগে। দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়। বস্তুত, বছরের পর বছর যায়। ধৈর্যের ফিক্সড ডিপোজিট ভাঙতে ভাঙতে পুঁজি একসময় তলানিতে এসে ঠেকে।
তবু মাঠ ছাড়া যায় না। পুরো প্রক্রিয়াটায় লেগে থাকতে হয় শেষ বাঁশি বাজা পর্যন্ত। কিনারার কেরামতি অর্থহীন, যদি না দোষী সাব্যস্ত করা যায় অপরাধীকে। বিচারে যদি ছাড়া পেয়ে যায় অভিযুক্ত, দিনের শেষে হাতে পেনসিলও পড়ে থাকে না। ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায়, প্রি-টেস্টে স্টার মার্কস, টেস্টে সব সাবজেক্টে লেটার, কিন্তু মাধ্যমিকে গিয়ে কম্পার্টমেন্টাল।
.
৩০ অগস্ট, ২০০১, যেদিন রায় বেরবে।
আদালত চত্বরে ঢুকেই খটকা লাগে অতনুর। সাদা পাঞ্জাবি-পাজামা পরা একদল যুবকের জটলা এজলাস কক্ষের বাইরে। চেহারায় উগ্রতা, হইহই আড্ডা দিচ্ছে অভিযুক্তদের আইনজীবীর সঙ্গে। বুঝতে অসুবিধে হয় না, এরা বামার আশ্রয়পুষ্ট খুচরো মস্তান। সে হোক, কিন্তু এত ফুর্তি কীসের, আর এত সাজগোজের ঘটাই বা কেন? শাস্তি যাদের আসন্ন, তাদের কাছের লোকদের মুখ চুন করে আদালতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এসেছেন এতদিন। আজ উলটপুরাণ?
কেন ফুর্তি, কেন সাজগোজ, রায়দান শুরু হতেই বুঝতে পারেন অতনু। হতভম্ব হয়ে যান দেখে, আটের দশকের সেই দুই কুখ্যাত পাকিস্তানি আম্পায়ার শাকুর রানা আর খিজার হায়াতকেও লজ্জা দিচ্ছে বিচারকের বক্তব্য। অভিযুক্তদের পক্ষে যিনি যুক্তিজাল সাজাচ্ছেন দৃষ্টিকটু রকমের একপেশে।
গুলিই যদি চলেছিল, কার্তুজের খোল পাওয়া গেল না স্পটে? এই দিয়ে শুরু। সওয়াল-জবাবের সময়ও এ প্রশ্ন উঠেছিল। সরকারি আইনজীবী বলেছিলেন, ‘হ্যাঁ, খোল পাওয়া যায়নি, ঠিকই। কিন্তু তা থেকে গুলি চলেইনি, এটা ভাবা সরলীকরণ হবে। ওইরকম জনবসতিপূর্ণ জায়গা। বোমা-গুলি চলার অন্তত আধঘণ্টা পর পুলিশ এসেছে। আগে গণ্ডগোল সামলেছে। ঘটনার দেড়-দু’ঘণ্টা পরে ভাল করে দেখতে পেরেছে ঘটনাস্থল। যেখানে কমপক্ষে দু’-তিনশো লোক আসা-যাওয়া করেছে তার আগে। খোল কার পায়ের ধাক্কায় কোথায় ছিটকে পড়েছে হয়তো। পাওয়া যায়নি। হতেই তো পারে, অসম্ভব কি?’ রায়ে বিচারক উড়িয়ে দিলেন সেই যুক্তি। লিখলেন, ঘটনায় আদৌ ব্যবহৃতই হয়নি আগ্নেয়াস্ত্র। পুরোটাই সাজিয়ে বলেছে প্রত্যক্ষদর্শীরা।
কেন সাজিয়ে বলবে? বিচারকের রায়ে যুক্তি, নিহিত স্বার্থের জন্য বলবে। উদয়ের দলের সঙ্গে ব্যবসায়িক শত্রুতা তৈরি হয়েছিল বামার দলের। উদয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপের ছেলেদের ফাঁসানোর এই সোনার সুযোগ হাতছাড়া করেনি রঞ্জিত-নিতাই এবং অকুস্থলে উপস্থিত উদয়ের অনুগামীরা। এদের বয়ানের উপর কোনওভাবেই নির্ভর করা চলে না। উদয়কে মেরেছে অন্য কোনও দল, অন্য আততায়ীরা। বামার দল নয়। আর, উদয়ের যা পূর্বইতিহাস, শত্রুসংখ্যা অনেক হওয়াটাই স্বাভাবিক। খুনের মামলা চলছে এখনও উদয়ের নামে। এই লোক অনেকেরই টার্গেট হতে পারে। রঞ্জিত নিজের ভাই, আর নিতাই বহু বছরের কর্মী। প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে এদের সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়।
দোসার দোকানের কর্মচারী বাচ্চু বিচারপর্বে ‘hostile witness’-এর (বিরূপ সাক্ষী) ভূমিকা নেওয়ায় ‘সাজানো গল্পের’ তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে সুবিধে হয়েছিল বিচারকের। বাচ্চু পুলিশকে বলেছিলেন, অভিযুক্তদের দেখলে চিনতে পারবেন। Test Identification Parade-এ বেমালুম অস্বীকার করেছিলেন বামা-টুটিদের চিনতে। অতনু অনেক পরে জানতে চেয়েছিলেন এই ভোলবদলের কারণ। বাচ্চু করজোড়ে জানিয়েছিলেন, ‘উপায় ছিল না স্যার। সাক্ষ্য দেওয়ার আগের দিন বামার দলের ছেলেপুলেরা বাড়িতে এসে বলে গিয়েছিল, “কোর্টে উলটোসিধে বললে বাড়ি জ্বালিয়ে দেব।”’
কিন্তু গণপিটুনিতে রিভলভার সমেত বাদলের আহত হওয়া? এসএসকেএম-এর ডাক্তারের কাছে দেওয়া বয়ান, ‘আমাকে ধাওয়া করে প্রচণ্ড মেরেছে কিছু লোক।’ নস্যাৎ করে দেওয়া হল রায়ে। বলা হল, পুরোটা পুলিশ বানিয়েছে। না হলে পুলিশ বাদলের গণপিটুনির ব্যাপারে একজনও প্রত্যক্ষদর্শীকে আদালতে হাজির করাতে পারল না কেন? বাদল যেটা বলেছে বিচারপর্বে, সেটাই বরং বিশ্বাসযোগ্য। কী? না, পুলিশ কেস সাজাতে বাদলকে তার বাড়ি থেকে তুলে এনে মারধর করে রিভলভার গুঁজে দিয়েছে। ডাক্তারের কাছে কী বয়ান দিতে হবে, সেটা শিখিয়েছে। কথা না শুনলে পুরো পরিবারকে মিথ্যে কেসে জড়িয়ে দেবে বলে শাসিয়েছে। আসলে বাদল স্পটে ছিলই না। বামা-পটা-টুটিও ছিল না।
তা হলে কারা মারল উদয় আর নরেশকে? বিচারকের জবাব তৈরিই ছিল রায়ে। এক ভদ্রলোকের সেলুন ছিল ঘটনাস্থলের ফুটবিশেক দূরে। চার্জশিটে তাঁকে সাক্ষী করেছিলেন অতনু। জেরার সময় অভিযুক্তদের আইনজীবী প্রচুর প্রশ্ন করেছিলেন নেহাতই সাদাসিধে সেলুনমালিককে। যার একটা ছিল, ‘বোমের আওয়াজ শুনেছিলেন যখন, তারপর কোনও গাড়ি যেতে দেখেছিলেন সেলুনের পাশ দিয়ে?’ কত গাড়িরই তো যাতায়াত ওই রাস্তা দিয়ে প্রতি মিনিটে। উত্তরে ভদ্রলোক বলেছিলেন, ‘হ্যাঁ, গাড়ি তো গিয়েছিল একটা বোমের আওয়াজ শোনার পর।’
কিমাশ্চর্যম, সব বাদ দিয়ে শুধু এই সাক্ষ্যকেই হাতিয়ার করে বিচারক রায়ে লিখলেন, আসলে অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীরা গাড়ি করে এসে বোমা মেরে পালিয়েছে। মিথ্যে কেস সাজিয়ে অভিযুক্তদের ফাঁসানোর অপচেষ্টার জন্য ভর্ৎসনা প্রাপ্য তদন্তকারী অফিসারের।
সুতরাং, ‘after considering all the evidences, oral and documentary, I am of the view that prosecution has failed to prove that the accused persons have committed the murder beyond reasonable doubt.’ বামা-পটা-টুটি বেকসুর খালাস। শাস্তি শুধু বাদলের, অস্ত্র আইনে। মাত্র দু’বছরের কারাদণ্ড।
অতঃপর বেকসুর খালাস, আলিপুর কোর্টে আবির-উৎসব এবং বাক্রুদ্ধ অতনুর প্রতি যথেচ্ছ শ্লেষ-বিদ্রুপ-কটাক্ষ। লালবাজার ‘ফুটে ফুলকপি!’
এতটাই হতোদ্যম হয়ে পড়েছিলেন অতনু, প্রায় ডিপ্রেশনে চলে যাওয়ার অবস্থা হয়েছিল। সাহস জুগিয়েছিলেন নগরপাল স্বয়ং, সিদ্ধান্ত হয়েছিল রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে যাওয়ার। ফের শুরু হয়েছিল লড়াই। যে লড়াইয়ে ফের ধৈর্য বন্ধক রাখতে হয়েছিল, যে লড়াই স্থায়ী হয়েছিল প্রায় পাঁচ বছরের কাছাকাছি। শেষমেশ হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ একত্রিশ পাতার রায়ে তুলোধোনা করেছিলেন নিম্ন আদালতের রায়কে। স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, আগের রায় ছিল প্রভাবিত এবং পূর্বনির্ধারিত, ‘and we believe it will not be unfair on our part if we bring on record that appreciation of evidence done by the learned Judge was, in fact, perverse and in a preconceived manner’… বদলে গিয়েছিল রায়। অতনুর যুক্তিজাল পূর্ণ সমর্থন পেয়েছিল হাইকোর্টের বিচারকদের। যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডিত হয়েছিল চার অভিযুক্ত।
হাইকোর্টের রায় বেরিয়েছে একটু আগে। অতনু বেরিয়ে আসেন আদালত চত্বর থেকে। পৌনে পাঁচটা বাজে। বিকেল একটু একটু করে সন্ধেকে জায়গা করে দিচ্ছে ড্রেস রিহার্সালের। গাড়ি ছেড়ে দেন অতনু। কতটাই বা দূরত্ব হাইকোর্ট থেকে লালবাজারের? মাথাটা হালকা লাগছে বহুদিন পর। হাঁটা যাক আজ। বেরনোর মুখে শুনেছেন, অভিযুক্তদের আইনজীবী বলছেন সদম্ভে, সুপ্রিম কোর্টে যাবেন। সে যান। আইনের উপর ভরসা ফিরে এসেছে আজকের রায়ে। যাক না ওরা সুপ্রিম কোর্টে, যাক না!
সুপ্রিম কোর্ট সম্পূর্ণ সহমত পোষণ করেছিল হাইকোর্টের রায়ের সঙ্গে। ফের সমালোচিত হয়েছিল নিম্ন আদালতের বিচার।
বলা হয়, জাস্টিস ডিলেইড ইজ় জাস্টিস ডিনায়েড। ন্যায়বিচারে দেরির অর্থ ন্যায় থেকে বঞ্চিত হওয়াই। ভুল, এই মামলার চূড়ান্ত পরিণতিতে মনে হয়েছিল অতনুর (বর্তমানে গোয়েন্দা বিভাগেরই অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার)। দেরি হয়েছিল, অনেকটাই দেরি হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হতে হয়নি শেষমেশ। বহু চড়াই-উতরাইয়ের পর মিলে গিয়েছিল অপরাধ আর শাস্তির হিসেব। মনে হয়েছিল অতনুর, কেউ না কেউ বোধহয় সবার অলক্ষ্যে জীবনের পাওনাগন্ডার ব্যালান্সশিটে নজর রাখেন আগাগোড়া, দিনের শেষে সব মিলিয়ে দেবেন বলে।
মেলাবেন তিনি মেলাবেন!
২.০৩ ‘দরজা ভাঙলেই গুলি করব!’
[আকুঞ্জি মামলা
বিমল সাহা, অবসরপ্রাপ্ত সহ নগরপাল। যথাক্রমে ১৯৯৮ এবং ২০০৮ সালে পেয়েছেন ভারত সরকারের ‘ইন্ডিয়ান পুলিশ মেডেল’ এবং ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদত্ত পদক।
আমিনুল হক, অবসরপ্রাপ্ত সহ নগরপাল, ১৯৯৯ সালে পেয়েছেন ভারত সরকারের ‘ইন্ডিয়ান পুলিশ মেডেল’।
রাম থাপা, বর্তমানে বড়তলা থানার ওসি, ২০০৪ সালে পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রদত্ত ‘সেবা পদক’।
তরুণকুমার দে, ইনস্পেকটর। গোয়েন্দাবিভাগ।
ইন্দ্রনীল চৌধুরী, বৰ্তমানে হেয়ার স্ট্রিট থানার ওসি। ২০০৪ সালে পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ‘সেবা পদক’, ২০১৮ সালে সম্মানিত হয়েছেন ভারত সরকারের ‘ইন্ডিয়ান পুলিশ মেডেল’-এ।
শাকিলুর রহমান, স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চে সহ নগরপাল হিসাবে কর্মরত।
তপন সাহা, পোর্ট ডিভিশনে সহ নগরপাল পদে কর্মরত।]
তু চিজ বড়ি হ্যায় মস্ত মস্ত
তু চিজ বড়ি হ্যায় মস্ত
তু চিজ বড়ি হ্যায় মস্ত মস্ত
তু চিজ বড়ি হ্যায় মস্ত…
নয়ের দশকের সেই সুপারহিট গান। লাস্যময়ী রবিনা ট্যান্ডনের লিপে। বাজছে ফুল ভলিউমে। তালে তালে উদ্দাম নাচছেন এক স্বল্পবাস সুন্দরী। যাঁর শরীরী বিভঙ্গের চুম্বক আচ্ছন্ন রেখেছে দর্শকদের। যিনি নাচতে নাচতেই উড়ন্ত চুমু ছুড়ে দিচ্ছেন মোহিনী ভঙ্গিতে। উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ছে নিশিবাসর। ঠোক্কর লাগছে গ্লাসে-গ্লাসে। চিয়ার্স! উল্লাস!
ম্যানেজার ব্যস্তসমস্ত তদারকিতে। মধ্য কলকাতার এই বার-কাম-রেস্তোরাঁয় প্রায় দশ বছর হয়ে গেল তাঁর। মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্তদেরই ভিড় মূলত এখানে। ‘পুশ-পুল’ লেখা সুইংডোর নেই। এসি নেই। ফটফট করে ইংরেজি-বলা ওয়েটার নেই। যা যা থাকে অভিজাত এলাকার নিশিনিলয়ে, তার কিছুই নেই। তবু শনিবার সন্ধে হলেই স্বল্প পরিসরের এই বার কালো মাথায় টইটম্বুর। রাত ন’টার পর এখানে টেবিল খালি পাওয়া আর রাজ্য লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ়ের মধ্যে তফাত নেই বিশেষ।
—এক মিনিট শুনবেন?
ম্যানেজার ফিরে তাকান প্রশ্নকর্তার দিকে। মধ্যতিরিশের এক সপ্রতিভ যুবক। চোখে রিমলেস চশমা।
—হ্যাঁ বলুন, জায়গা তো এখন দেখছেনই খালি নেই। বাইরে অপেক্ষা করতে হবে।
যুবক হাসেন। গানবাজনা চলছে যা তারস্বরে, হ্যান্ডশেকের দূরত্বেও একে অন্যের কথা শুনতে পাওয়া দুষ্কর। যুবক কানের কাছে মুখ নামিয়ে আনেন ম্যানেজার ভদ্রলোকের, কিছু একটা বলতে। শোনামাত্র মুখের ভাব বদলে যায় ম্যানেজারের। দ্রুতপায়ে পৌঁছে যান বারের এক প্রান্তের কাঠের পাটাতনের কাছে। যেখানে কোমর দোলাচ্ছেন সুন্দরী যুবতী, গানের সঙ্গে সঙ্গত করতে বসে আছেন বাদ্যযন্ত্রীরা।
গানটা শেষ হওয়ার যা অপেক্ষা। যুবতীর কানে ফিসফিস করেন ম্যানেজার। ত্রস্ত পায়ে মঞ্চ থেকে নেমে আসেন যুবতী। স্বল্পবেশেই বেরিয়ে আসেন বাইরে। চশমা-পরা যে যুবক একটু আগে ম্যানেজারকে কানে কানে কিছু বলার পরই এইসব, তিনিও ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছেন বাইরে। এবং তাঁর পাশে উদয় হয়েছেন শক্তসমর্থ চেহারার আরও চারজন। যাঁদের মধ্যে দু’জন মহিলা।
সোজাসুজি নির্দেশ জারি করেন রিমলেস চশমার যুবক, নর্তকী যুবতীর চোখে চোখ রেখে।
—আপনাকে একবার আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।
যুবতী হতভম্ব। বিস্ময়ের ঘোর কাটতে সময় লাগে একটু।
—মানে? যেতে হবে মানে? কোথায় যেতে হবে? আপনারা কারা? কোথা থেকে আসছেন?
—লালবাজার।
.
.৩৮ রিভলভার। লোডেড। বুশ শার্টের নীচে কোমরে গোঁজা রয়েছে ওঁদের।
‘ওঁদের’ মানে ওঁদের আটজনের। উর্দি পরে আসেননি কেউই। সবাই প্লেন ড্রেসে আজ।
ঘরের দরজায় কড়া নাড়ার আগে চোখাচোখি হয় ওঁদের। শুধু চোখাচোখিই। কথা হয় না কোনও। যা কথা হওয়ার, হয়ে গেছে আগে। কী কথা?
ঘরের ভিতর যারা আছে, তারা অত্যন্ত মারাত্মক প্রকৃতির। বেপরোয়া। সামান্যতম বিপদের গন্ধ পেলেই ধুমধাড়াক্কা গুলি চালাবে। বাড়তি সতর্কতা প্রয়োজন। তেমন বুঝলে সঙ্গে সঙ্গে পালটা গুলি চালাতে হবে। ঘরে ঢোকার এবং বেরনোর এই একটাই রাস্তা। অনেক ভুগিয়েছে এরা। হাড়মাস কালি করে দিয়েছে। যা-ই হয়ে যাক, পালাতে দেওয়া যাবে না। হয় এসপার, নয় ওসপার।
মাঝরাত পেরিয়ে ঘড়িতে প্রায় তিনটে। এমন একটা সময়, যখন স্ট্রিট লাইটগুলো পর্যন্ত সামান্য স্তিমিত। ঢুলছে। এমন একটা সময়, যখন রাস্তার কুকুরগুলোও সাময়িক স্থগিত রেখেছে অপরিচিত আগন্তুক দেখলেই ‘ঘেউ ঘেউ’। জিরিয়ে নিচ্ছে দু’দণ্ড। পাড়া জাগিয়ে চিলচিৎকার করার সময় পরে অনেক পাওয়া যাবে।
ভেবেচিন্তেই বাছা হয়েছে সময়টা। নির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে কোনও দুর্ধর্ষ অপরাধীর আস্তানায় রেইড করতে গেলে ওটাই মাহেন্দ্রক্ষণ। ওটাই ব্রাহ্মমুহূর্ত। যাকে ধরতে যাওয়া, তার ঘুমিয়ে থাকার সম্ভাবনা থাকে প্রবল। আর একটা সুবিধে, আশেপাশের বাড়ি-ঘরদোরেও ঘুমিয়ে থাকেন বাসিন্দারা। রাস্তা থাকে শুনশান। পুলিশের গতিবিধির আগাম খবর অপরাধী পেয়ে যাবে স্থানীয় সূত্রে এবং চম্পট দেবে, সে আশঙ্কাও থাকে না বড় একটা।
কড়া নাড়া হল দরজায়। নেড়ে দরজার দু’পাশে ভাগ হয়ে গেলেন ওঁরা। সিনেমায় যেমন হয়। একদিকে চার, অন্যদিকে বাকি চার। উত্তর নেই ভিতর থেকে। ফের ঠক্ ঠক্ দরজায়। এবার জবাব এল।
—কে?
—পুলিশ। লালবাজার থেকে আসছি। দরজাটা খুলুন। দরকার আছে।
সেকেন্ড দশেকের নীরবতার পর ভিতর থেকে ফের ছিটকে এল উত্তর। গলার স্বরে মরিয়া ভাবটা স্পষ্ট।
—পুলিশ হোক আর যে-ই হোক, ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করলেই গুলি করব।
গুলি করার হুমকি যে ফাঁকা আওয়াজ নয়, জানতেনই ঘরের বাইরে থাকা অফিসাররা। যাঁদের কোমরে গোঁজা আগ্নেয়াস্ত্র হাতে উঠে এল নিমেষে। ট্রিগার স্পর্শ পেল আঙুলের।
দরজা যে ভাঙতে হতে পারে, সেটাও জানার মধ্যেই ছিল। এবং ছিল প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিও। শাবল-গাঁইতি আনা হয়েছিল ব্যাগে করে।
প্রয়োজন হল না অবশ্য। তেমন পোক্ত দরজা নয়। সজোরে গোটা দশেক লাথিতেই কলকবজা দেহ রাখল। এবং সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে ছুটে এল গুলি। কাঁধ চেপে বসে পড়লেন এক অফিসার। পালটা গুলি চালানো ছাড়া উপায় কী আর?
সত্যিই এসপার-ওসপার!
.
—অনেক আলোচনা হয়েছে। আমি জাস্ট একটা প্রশ্ন করে মিটিং শেষ করব!
নগরপালের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকান লালবাজারের কনফারেন্স রুমে উপস্থিত অফিসাররা। কী প্রশ্ন? থেমে থেমে ঠান্ডা গলায় বলতে থাকেন সিপি।
—হোয়াট নেক্সট? আমরা কি ছ’নম্বর ডাকাতিটার জন্য অপেক্ষা করব? আর ছয়ের পর সাত নম্বরের জন্য?
লালবাজারের কনফারেন্স রুমে নিশ্ছিদ্র নীরবতা নেমে আসে। পিন পড়লেও মনে হবে, চকলেট বোম ফাটল বুঝি। গোয়েন্দা বিভাগের Anti-dacoity বিভাগের সমস্ত অফিসার উপস্থিত। আছেন ডিসি ডিডি। সবার ঠোঁটে যেন সাইলেন্সার লাগিয়ে দিয়েছে কেউ।
কী-ই বা বলবেন ওঁরা সিপি-র প্রশ্নের উত্তরে? বলার মুখ থাকলে তো বলবেন! তিন মাসের মধ্যে পাঁচ-পাঁচটা ডাকাতি শহরের বুকে! এবং ডাকাতদের ধরা তো দূরস্থান, চিহ্নিতই করা যায়নি এখনও। অথচ জুলাইয়ের তৃতীয় সপ্তাহে যখন প্রথম ডাকাতিটা হয়েছিল, গোয়েন্দারা দূরতম কল্পনাতেও ভাবেননি, পরের কয়েক মাসে তাঁরা পেশাগত জীবনের কঠিনতম চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে যাচ্ছেন।
.
১৯ জুলাই, ১৯৯৭। শনিবার। ট্যাংরা অঞ্চলের ৫২ডি, রাধানাথ চৌধুরী রোডের ফেডারাল ব্যাংকে কোলাপসিবল গেট বন্ধ করার প্রস্তুতি চলছে। বেলা বারোটা প্রায় বাজতে চলল। শনিবার গ্রাহকদের জন্য ব্যাংক বন্ধ হয়ে যায় বারোটায়। জনাচারেক গ্রাহক এখনও কাউন্টারে আছেন। ওঁরা কাজ সেরে বেরিয়ে গেলেই ঝাঁপ ফেলে দেওয়া হবে রুটিনমাফিক।
কোথায় কাউন্টার বন্ধ করা, আর কোথায় ঝাঁপ ফেলা! বারোটা বাজার আগেই ব্যাংকের মধ্যে হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল ছ’জন যুবক। যাদের চারজনের হাতে রিভলভার। বাকিদের হাতে ছুরি। যে চারজন গ্রাহক ক্যাশ কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাঁদের দিকে রিভলভার তাক করে আদেশ দিল এক যুবক।
—একটাও শব্দ করবেন না। করলে জানে মেরে দেব। চুপচাপ ওখানে গিয়ে বসে থাকুন। যান ওখানে!
‘ওখানে’ মানে দেওয়ালের এক কোণে। কাঁপতে কাঁপতে সেখানে গিয়ে বসে পড়লেন চারজন। পাহারায় সামনে দাঁড়িয়ে রইল রিভলভারধারী।
ততক্ষণে ব্যাংকের ল্যান্ডলাইনের তার কেটে দিয়েছে যুবকের দল। দুই ক্যাশিয়ারকে টেনে বার করে এনেছে কাউন্টারের ভিতর থেকে। এবং টাকার গোছা গোছা বান্ডিল তিন যুবক ভরতে শুরু করেছে সঙ্গে আনা থলেতে।
ব্রাঞ্চ ম্যানেজার রামচন্দ্রন নায়ার আর দুই অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার গণপতি পেরুমল এবং সি জে অগাস্টিন হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন কেবিন থেকে। বাইরে কিছু একটা গণ্ডগোলের আভাস পেয়ে, চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে। দুই যুবক নিমেষে রিভলভার মাথায় ঠেকিয়ে দিল রামচন্দ্রন আর পেরুমলের। অগাস্টিন থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে নিজেই মাটিতে বসে পড়লেন।
ব্রাঞ্চ ম্যানেজারের মাথায় রিভলভার ধরে এরপর স্ট্রংরুমে নিয়ে যাওয়া, ভল্ট খোলানো এবং ডাকাতদলের থলি দ্রুত ভরতি হয়ে যাওয়া টাকার বান্ডিলে। রামচন্দ্রন কিছু একটা বলতে গেলেন। ‘বারণ করলাম না শব্দ করতে?’ বলে রিভলভারের বাঁট দিয়ে সজোরে ভদ্রলোকের কপালে আঘাত করল এক যুবক। রক্তপাত অঝোরে। ব্যাংকের সমস্ত কর্মচারী নিথর বসে রইলেন নিজের নিজের চেয়ারে। চোখেমুখে প্রবল আতঙ্কের আঁকিবুকি নিয়ে।
আধঘণ্টার মধ্যে অপারেশন কমপ্লিট। আট লক্ষ আটচল্লিশ হাজার টাকা লুঠ করে তিনটে মোটর সাইকেলে সওয়ার হয়ে উধাও ডাকাতরা। এন্টালি থানার অফিসাররা যখন খবর পেয়ে এলেন, যখন এসে পৌঁছলেন গোয়েন্দা বিভাগের কর্তারা, তখনও আতঙ্কের ঘোর কাটেনি এলাকায়। তখনও ঘটনার বিবরণ দিতে গলা কাঁপছে ব্যাংকের কর্মচারীদের।
পোশাক কেমন ছিল?— হাফ শার্ট আর ট্রাউজার। চেহারা?— মাঝারি হাইট এবং দোহারা গড়ন সবারই। একজন ছাড়া। যে তুলনায় বেঁটে, মোটাসোটা। রামচন্দ্রনের ভাষায়, ‘hefty and bulky’।
কী ভাষায় কথা বলছিল?— পরিষ্কার জড়তাহীন বাংলায়।
কেউ কাউকে নাম ধরে ডেকেছিল, যতক্ষণ ব্যাংকের মধ্যে ছিল? —না।
কারও চেহারায় কোনও বিশেষত্ব চোখে পড়েছিল? টাকমাথা বা গালে আঁচিল? কপালে কাটা দাগ বা টেনে টেনে হাঁটা? কোনও কিছু এমন, যা দিয়ে আর পাঁচজনের থেকে আলাদা করা যায়? — না, তেমন তো কিছু মনে পড়ছে না!
বয়স? —এই পঁচিশ-তিরিশের মধ্যে হবে আন্দাজ। শুধু ওই বেঁটে মোটা লোকটাকে দেখে বয়স সামান্য বেশি বলে মনে হয়েছে।
আবার দেখলে ওদের চিনতে পারবেন? —হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা ডেফিনিটলি পারব।
.
ভারতীয় দণ্ডবিধিতে অপরাধের স্তরবিভেদ আছে। Offences against body, অর্থাৎ শারীরিক আঘাতজনিত অপরাধ। খুচরো মারামারি থেকে শুরু করে খুন পর্যন্ত। Offences against property, সম্পত্তির ক্ষতি সংক্রান্ত অপরাধ। পকেটমারি, ছিঁচকে চুরি থেকে ডাকাতি পর্যন্ত।
সম্পত্তিজনিত অপরাধের তালিকায় শীর্ষবাছাই, লেখা বাহুল্য, ডাকাতিই। Offences against property-র মধ্যে সাধারণভাবে কোন অপরাধকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত? বিশ্বের সমস্ত পুলিশ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের এই প্রশ্নের জবাবে তিন অক্ষরের একটা শব্দই বরাদ্দ থাকে। ডাকাতি।
কেন, সহজবোধ্যই। একটা খুন হওয়ার নানারকম কারণ থাকতে পারে। সে টাকার লোভ বলুন, ব্যক্তিগত দ্বেষ বলুন, প্রেমঘটিত আক্রোশ বলুন বা যৌন-ঈর্ষা। কারণ সে যা-ই হোক, একটা বিচ্ছিন্ন খুন সামগ্রিকভাবে আমার-আপনার মধ্যে নিরাপত্তাবোধের তীব্র অভাব জাগিয়ে তোলে না। কিন্তু ডাকাতি? পাড়ায় যদি একটা দুঃসাহসিক ডাকাতি হয়ে যায়, মারধর করে লুঠপাট চালিয়ে যায় ডাকাতরা? প্রতিবেশীদের মনে অবধারিত তৈরি হয় ভয় আর আতঙ্কের যুগলবন্দি। কাল ওই বাড়িটায় হয়েছে, পরশু যে আমার বাড়িতে হবে না, কী গ্যারান্টি?
এই কারণেই ভারতীয় দণ্ডবিধিতে ‘ডাকাতি’-র চারটি পর্যায় চিহ্নিত করে শাস্তির বিধান রয়েছে। ডাকাতির জন্য জড়ো হওয়া। ডাকাতির জন্য অস্ত্রশস্ত্র সমেত প্রস্তুতি নিয়ে একত্রিত হওয়া। ডাকাতির চেষ্টা। এবং ডাকাতি সংঘটিত করা।
ডাকাতির মধ্যে আবার চরিত্রভেদ রয়েছে। বাড়িতে হতে পারে। দোকানে হতে পারে। পথচলতি গাড়ি থামিয়ে হতে পারে। কিনারা করা কতটা দুরূহ, সেটা যদি মানদণ্ড হয়, তবে পুলিশের কাছে সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং হল ব্যাংক-ডাকাতি।
কেন তুলনায় বেশি চ্যালেঞ্জিং? গোপন কিছু নয়। দুর্বোধ্যও নয়। প্রথমত, সব ডাকাত ব্যাংক-ডাকাত নয়, কেউ কেউ ব্যাংক-ডাকাত। ব্যাংক-ডাকাতি একটা ‘specialized crime’, বাড়ি-গাড়ি-দোকানে ডাকাতির থেকে আলাদা। অন্য কোথাও ডাকাতির তুলনায় অনেক বেশি ঝুঁকি আর সাহস লাগে ব্যাংকলুঠে। যা করতে হয়, দিনের বেলায় করতে হয় ডাকাতদের। রাতবিরেতে আচমকা হানা দিয়ে কাজ হাসিল করার গল্প নেই কোনও। এবং যেহেতু দিনের বেলায়, যেহেতু গ্রাহক এবং কর্মীদের উপস্থিতিতে দুষ্কর্ম, ধরা পড়ে যাওয়ার চান্স ঢের বেশি। চিহ্নিত হয়ে যাওয়ার চান্স বেশি। ডাকাতির সময় প্রতিরোধের মুখে পড়লে কী করব, লুঠের পর কীভাবে কোন রাস্তা দিয়ে কোথায় পালাব যত দ্রুত সম্ভব, কোথায় কীভাবে গা ঢাকা দেব, লুঠের টাকা কার কাছে কতটা থাকবে, সব নিখুঁত ভেবে রাখতে হয় আগে থেকে। সামান্য ভুলচুক হলেই ভরাডুবি অনিবার্য এবং শ্রীঘরযাত্রা।
দ্বিতীয়ত, কোনও বাড়ি বা দোকানে অতর্কিত হামলা করে ‘আলমারির চাবি কোথায়?’ বলা আর ভয় দেখিয়ে টাকাপয়সা-গয়নাগাটি কেড়ে নেওয়ার তুলনায় ব্যাংকলুঠ অনেক বেশি কঠিন। প্রথমটা পাস কোর্স হলে দ্বিতীয়টা অনার্স। আগে থেকে ব্যাংকের অবস্থানগত খুঁটিনাটি জেনে রাখতে হয়। সরেজমিনে দেখে যেতে হয় একাধিকবার। যাকে বলে recce করা।
ঢোকা-বেরনোর গেট কতটা প্রশস্ত, ক’টা ক্যাশ কাউন্টার, কতজন কর্মী, কে কোথায় বসেন, ম্যানেজারের ঘর কোনটা, স্ট্রং রুম কোথায়, সব মাথায় রেখে তবে প্ল্যান করে ব্যাংক-ডাকাতরা। এবং সবচেয়ে জরুরি, ব্যাংকে চড়াও হওয়ার সময়টা। পুরনো রেকর্ড খতিয়ে দেখলে বোঝা যায়, হয় ব্যাংক খোলার সময়, বা বন্ধ হওয়ার সময়, বা ভরদুপুরে সিংহভাগ ব্যাংক-ডাকাতি ঘটে থাকে। এমন একটা সময়ে, যখন গ্রাহকের ভিড় জমাট বাঁধেনি ব্যাংকে। দিনের শুরু বা শেষে যখন কর্মীরাও একটু অগোছালো, একটু ঢিলেঢালা। পেশাদারি প্ল্যানিংয়ে অপরাধটা হয় বলেই ব্যাংক-ডাকাতির কিনারা দুরূহতর হয়ে দাঁড়ায় তুলনামূলক ভাবে।
ফেডারাল ব্যাংকের ডাকাতিটার পর প্রথাসিদ্ধ পথেই এগিয়েছিল গোয়েন্দা বিভাগ। এক, ব্যাংকের কর্মী এবং গ্রাহক যাঁরা ঘটনার সময় উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের বিবরণ অনুযায়ী ব্যাংক-ডাকাতদের ছবি আঁকানো, ‘Portrait Parle’। এবং আঁকানোর পর সেই ছবি মিলিয়ে দেখা অতীতে ধরা পড়া ব্যাংক-ডাকাতদের সঙ্গে। ছবি ছড়িয়ে দেওয়া সোর্সদের মধ্যে। সোর্সদের ভূমিকায় পরে আসছি বিস্তারিত। এক লাইনে সেরে দেওয়া যাবে না এই কাহিনিতে।
দুই, শহরে তো বটেই, গত দশ বছরে রাজ্যের সমস্ত ব্যাংক-ডাকাতির রেকর্ড দেখা খুঁটিয়ে। যারা ধরা পড়েছিল পুরনো মামলায়, তাদের ছবির সঙ্গে কোনও মিল আছে ডাকাতদের? পুরনো গ্যাংগুলোর ‘মোডাস অপারেন্ডি’-র সঙ্গে কোনও সাদৃশ্য? পুরনো কেসে ধৃত ডাকাতদের কারা কারা এখন জামিনে জেলের বাইরে? কী তাদের গতিবিধি? দস্যু রত্নাকর থেকে বাল্মীকিতে রূপান্তরের ঘটনা বাস্তবে তো আর খুব বেশি ঘটে না!
চেষ্টায় ত্রুটি ছিল না anti-dacoity বিভাগের অফিসারদের। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও সূত্র ছিল অমিল। প্রায় দু’মাস কেটে গিয়েছিল ট্যাংরার ডাকাতির পর। সমাধান ছিল অধরাই। এবং যত দেরি হচ্ছিল, প্রমাদ গুনছিলেন অফিসাররা। পুলিশে বলা হয়, ‘The best way to prevent the recurrence of a crime is to detect it.’ অপরাধের পুনরাবৃত্তিকে প্রতিহত করার সেরা রাস্তা একটাই। অপরাধের কিনারা করে ফেলা যথাসাধ্য দ্রুত। এক্ষেত্রে ‘ডিটেকশন’ এখনও দূর অস্ত। শহরে সরকারি-বেসরকারি মিলিয়ে কয়েকশো ব্যাংক। সর্বত্র সবসময় নজরদারি সম্ভব, সম্ভব এভাবে ‘প্রিভেনশন’? যা মনে হচ্ছে, নতুন কোনও গ্যাং। বেপরোয়া এবং মরিয়া। একটা ক্রাইম করে সাধারণত থেমে যায় না এরা।
থামলও না। ১৯ জুলাইয়ের পর ৬ সেপ্টেম্বর। ট্যাংরার পর আলিপুর। ফেডারাল ব্যাংকের পর স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। মোমিনপুর ব্রাঞ্চ। সকাল ১১-২৫ থেকে ১১-৪৫, কুড়ি মিনিটের অপারেশন একই কায়দায়। রিভলভারের বাঁটের আঘাত ব্যাংকের অ্যাকাউন্টেন্টের মাথায়। চার লক্ষ আট হাজার চারশো তেরো টাকা লুঠ করে ছ’জনের ডাকাতদল উধাও! একটা মারুতি এবং দুটো মোটরসাইকেলে করে।
আলিপুরের ডাকাতির সপ্তাহ তিনেক পরেই, ২৮ সেপ্টেম্বর, লেক থানা এলাকার স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার শাখায় হানা দিল ডাকাতরা। একটা বাজার পাঁচ মিনিট আগে। সেই পাঁচ-ছয় জনের দল, সেই একই পদ্ধতি। আচরণ অবশ্য হিংস্রতর। ব্যাংকের নিরাপত্তারক্ষী বাধা দিতে গেছিলেন, সটান গুলি চালিয়ে দিল এক ডাকাত। ভোজালির আঘাতে রক্ত ঝরল আরও তিনজন ব্যাংককর্মীর। গুলিবিদ্ধ নিরাপত্তারক্ষীকে এবং আহত হওয়া বাকিদের যখন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শরৎ বোস রোডের রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে, তখন বাজে প্রায় দেড়টা। যার পনেরো মিনিট আগে, সোয়া একটা নাগাদ তিন লক্ষ আটষট্টি হাজার টাকা লুঠ করে চম্পট দিয়েছে ডাকাত দল।
ডাকাতি নম্বর চার, অক্টোবরের ২০ তারিখ। এবার ব্যাংকে নয়। অরবিন্দ সরণির একটা দোকানে। নাম, ‘ইন্ডিয়া ট্রেডিং কোম্পানি’। দুপুর একটার পরে তিনটে মোটরসাইকেল এসে ব্রেক কষল দোকানের সামনে। দোকানের কর্মচারীদের রিভলভার দেখিয়ে ক্যাশবাক্স ভেঙে পাঁচ লক্ষ টাকা লুঠ। এবার রিভলভার-ভোজালির পাশাপাশি নতুন সংযোজন, বোমা। পালানোর আগে দুটো বোমা রাস্তায় ছুড়ল ডাকাতরা। স্প্লিন্টারের আঘাতে আহত হলেন দু’জন পথচারী। ডাকাতদের চেহারার বিবরণ? আশঙ্কা সত্যি হল, মিলে গেল আগের তিনটে ঘটনার সঙ্গে।
পঞ্চম ঘটনা নভেম্বরের সাত তারিখে। এবার টার্গেট সিইএসসি-র গাড়ি। যাচ্ছিল শ্যামবাজারের অফিস থেকে ধর্মতলার সদর দফতর ভিক্টোরিয়া হাউসে। গাড়িতে প্রায় ছাব্বিশ লক্ষ টাকা ছিল। ছিলেন সিইএসসি-র তিনজন কর্মী এবং এক বন্দুকধারী রক্ষী। দুপুর একটা নাগাদ মহাত্মা গাঁধী রোড আর চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউয়ের ক্রসিংয়ের কাছে ক্যাশভ্যানের পথ আটকে দাঁড়াল তিনটে মোটরসাইকেল। ড্রাইভারের মাথায় এরপর রিভলভার ঠেকানো, রক্ষীর বন্দুক কেড়ে নেওয়া, এক কর্মীর মাথায় রিভলভারের বাঁট দিয়ে মেরে রক্তপাত ঘটানো এবং পঁচিশ লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার চারশো বারো টাকা নিয়ে তিরবেগে উধাও হয়ে যাওয়া পাঁচ-ছ’জনের দলের। যাদের চেহারার বর্ণনা প্রত্যক্ষদর্শীদের থেকে শুনে পুলিশের সন্দেহের ন্যূনতম অবকাশও থাকল না, এরা ওরাই। একই গ্যাং। পাঁচজন মাঝারি হাইটের, দোহারা চেহারার। একজন বেঁটে, মোটাসোটা।
১৯ জুলাই, ৬ সেপ্টেম্বর, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০ অক্টোবর, ৭ নভেম্বর। চার মাসেরও কম সময়ের মধ্যে পাঁচটা দুঃসাহসিক ডাকাতি। লুঠ প্রায় পঞ্চাশ লাখের কাছাকাছি। যথেচ্ছ গুলি-বোমার ব্যবহার। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, নড়ে গিয়েছিল লালবাজার। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল শহরে। আশঙ্কা-উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ত্রিভুজে দমবন্ধ অবস্থা হয়েছিল গোয়েন্দা বিভাগের অফিসারদের। কারা এরা? এরপর কবে? কোথায়? কখন?
দীর্ঘ বৈঠকের পর লালবাজারের কনফারেন্স রুমে কটাক্ষের সুরে এই প্রশ্নটাই ছুড়ে দিয়েছিলেন সিপি।
—হোয়াট নেক্সট? আমরা কি ছ’নম্বর ডাকাতির জন্য অপেক্ষা করব? আর ছয়ের পর সাত নম্বরের জন্য?
সরকারের উপরমহলে ডাকাতির ঘটনাগুলোর দ্রুত সমাধানে কলকাতা পুলিশের ব্যর্থতার জবাবদিহি করতে করতে সাময়িক ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল সিপি-র। যদিও নগরপাল জানতেন বিলক্ষণ, কী প্রাণান্তকর চেষ্টা চালাচ্ছিলেন গোয়েন্দারা। যাঁদের কাছে দুটো ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল ডাকাতির ঘটনাগুলোর চুলচেরা পোস্টমর্টেমে।
এক, কলকাতার বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের ‘গ্যাং’ এরা। রাজ্যের বাইরের নয়। বিহারের ডাকাত-অধ্যুষিত গয়া-পাটনা-বেগুসরাই-জামুইয়ের নয়। স্পষ্ট বাংলায় কথা বলেছে প্রত্যেকটা ঘটনায়। খোঁজখবরের কেন্দ্রস্থল তাই হওয়া উচিত শহর আর আশেপাশের জেলায়।
‘আশেপাশে’ শব্দটা শুনলে এমনিতে মনে হয় কাছেপিঠেই। খুব দূরে নয়, এমন কোনও জায়গা যেন। এক্ষেত্রে কিন্তু নামেই শুধু ‘আশেপাশে’। আসলে হাজার হাজার বর্গকিলোমিটারের বিস্তীর্ণ এলাকা। উত্তর ২৪ পরগনায় ব্যারাকপুর মহকুমার টিটাগড়, জগদ্দল, নোয়াপাড়া, নৈহাটি, বীজপুর। বারাসত সংলগ্ন এলাকার মধ্যমগ্রাম, আমডাঙা, দেগঙ্গা। সঙ্গে যোগ করুন বসিরহাট এবং বনগাঁ মহকুমার ব্যাপ্ত ভূখণ্ড। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বারুইপুর-জয়নগর-কুলতলি-গোসাবা-বাসন্তী-ক্যানিং-ধামাখালি এবং সুন্দরবন সংলগ্ন অঞ্চল। হাওড়া-হুগলি তো আছেই। একদিকে সাঁতরাগাছি-ডোমজুড়-আন্দুল ইত্যাদি। অন্যদিকে চুঁচুড়া-পোলবা-ধনেখালি-মগরা-পাণ্ডুয়া-সিঙ্গুর-চণ্ডীতলা-জাঙ্গিপাড়া প্রভৃতি।
দুই, পাঁচটা ঘটনার একটাতেও মুখ ঢাকা ছিল না ডাকাতদের। অনেকেই দেখেছে চেহারাগুলো। মনে রেখেছে। অন্তত পঞ্চাশ-ষাট জনের সঙ্গে কথা বলে ছবি আঁকানো হয়েছে ছ’জনের। অথচ চিহ্নিত করা যায়নি। না পাওয়া গেছে পুরনো রেকর্ডে, না চিনতে পেরেছে সোর্সরা। নতুন গ্যাং, অথচ প্রতিটা ঘটনায় ‘এ টু জেড’ তুখোড় প্ল্যানিং। সিইএসসি-র টাকা কখন কোন রাস্তা দিয়ে শ্যামবাজার থেকে ধর্মতলা যাবে, খবর ছিল নিখুঁত। অরবিন্দ সরণির দোকানের ক্যাশবাক্স ভাঙলে যে প্রচুর টাকা পাওয়া যাবে, অজানা ছিল না ওদের।
ডাকাতদের ছবি আঁকানোর অবশ্য প্রয়োজনই হত না আজকের দিন হলে। সব ব্যাংকে সিসি টিভি আছে আজকাল। এক মিনিটে ফুটেজ চলে আসে হাতে। ঘটনা ১৯৯৭-এর। তখন না ছিল সিসি টিভি, না ছিল হাতে হাতে মোবাইল ফোন। ‘ইলেকট্রনিক ইনটেলিজেন্স’-এর সুবিধে থেকে বঞ্চিত ছিলেন সে-সময়ের তদন্তকারীরা। ভরসা ছিল শুধু ‘হিউম্যান ইনটেলিজেন্স’। সাদা বাংলায়, সোর্স।
সোর্স। যারা পুলিশকে খবর দেয়। কারা দেয়? অপরাধের খবর, অপরাধীর খবর কি ভারত সেবাশ্রম বা রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা দেবেন? অপরাধ-জগতের সঙ্গে যারা যুক্ত, অতীতে বা বর্তমানে, তারাই দেবে। তারাই দেবে খবর, অপরাধের সূত্রেই যাদের সঙ্গে কখনও কখনও যোগাযোগ হয়েছে পুলিশ অফিসারদের। যোগাযোগ থেকে ক্রমশ সম্পর্ক তৈরি হয়েছে খবর আদানপ্রদানের।
সোর্স তৈরি করা এবং তাকে লালন করা এক শিল্পবিশেষ। যা আয়ত্ত না করতে পারলে সফল গোয়েন্দা হওয়ার স্বপ্ন দিনের শেষে স্রেফ সোনার পাথরবাটিই। একজন বিশ্বস্ত সোর্স তৈরি করতে কখনও কখনও লেগে যায় এক বছর বা তারও বেশি। এবং এমনও আকছার হয়, সেই সোর্সের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অফিসারের ব্যক্তিগত স্তরে গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়ে যায়। অফিসারের বাড়ির কেউ অসুস্থ হয়েছেন, হয়তো বিরল গ্রুপের রক্তের প্রয়োজন। সবার আগে সেই সোর্স হাজির হয়ে যায়, ‘কী লাগবে স্যার, আমাকে বলুন।’ এবং প্রাণপাত দৌড়ঝাঁপে জোগাড় করে আনে নির্দিষ্ট গ্রুপের রক্তদাতা।
আবার সোর্সের পারিবারিক সুখদুঃখের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েন অফিসাররা। সে সোর্সের ছেলেমেয়েদের জন্য পুজোর জামা কিনে দেওয়াই বলুন বা তাদের স্কুলকলেজে ভরতি হওয়ার জন্য অর্থসাহায্য করা। অবসর নেওয়ার পরও বহু অফিসারের সঙ্গে সুসম্পর্ক থেকে যায় তাঁদের একসময়ের সোর্সদের। যে সম্পর্ক দাতা-গ্রহীতার ঊর্ধ্বে।
সোর্সকে ঠিকঠাক ‘হ্যান্ডল’ করতে না পারলে অবশ্য সেমসাইড গোলের সম্ভাবনা। সুযোগ পেলেই পুলিশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাকে অপব্যবহার করার প্রবণতা থাকে সোর্সদের একটা বড় অংশের। যারা মনে করে, পুলিশ অফিসারদের খবর দিই মানে অন্যত্র যা খুশি করার লাইসেন্স পাওয়া হয়ে গেছে।
অমুক জায়গায় হয়তো চোলাই মদের ঠেক বসেছে। তমুক জায়গায় হয়তো জুয়ার বোর্ড চলছে গোপনে। সোর্স গিয়ে টাকা আদায় করতে শুরু করে। না দিলে পুলিশকে জানিয়ে দেবে, এই ভয় দেখিয়ে। সোর্সকে তাই অনেক সময় ‘ম্যানমার্কিং’ করতে হয় অফিসারদের। এক সোর্সের পিছনে লাগাতে হয় অন্য সোর্স। যাতে কোনও সোর্স উইং দিয়ে ওভারল্যাপে গেলেই খবর আসে, এবং পত্রপাঠ থামিয়ে দেওয়া যায় কড়া ট্যাকলে। যাতে ‘সোর্স’ কোনভাবেই ‘রিসোর্স’ না হয়ে যায়।
পাঁচ সাব-ইনস্পেকটর তদন্ত করছিলেন ডাকাতির পাঁচটা মামলার। এন্টালির কেসের দায়িত্বে ছিলেন ইন্দ্রনীল চৌধুরী। আলিপুরের মামলায় তরুণকুমার দে। লেকের ব্যাংক ডাকাতির তদন্ত করছিলেন রাম থাপা। সিইএসসি-র টাকা লুঠের তদন্তকারী অফিসার ছিলেন তপন সাহা এবং অরবিন্দ সরণির দোকানে ডাকাতির তদন্তভার ন্যস্ত হয়েছিল শাকিলুর রহমানের উপর। তবে যেহেতু প্রতিটি ঘটনাই সংশয়াতীত ভাবে ছিল একই দলের কীর্তি, তদন্তকারী অফিসাররা একত্রে ঝাঁপিয়েছিলেন সমাধানে। সকলের মধ্যে সমন্বয়ের কাজটা করছিলেন anti-dacoity বিভাগের ওসি বিমল সাহা এবং অ্যাডিশনাল ওসি আমিনুল হক। তদন্তের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ, ছিল বিমল-আমিনুলেরই দায়িত্বে।
যার যেখানে যা সোর্স ছিল, প্রত্যেককে খবর পাঠানো হয়েছিল। নগরপাল ঢালাও বরাদ্দ করেছিলেন ‘সোর্সমানি’। নির্দেশ ছিল স্পষ্ট, সোর্সকে যেখানে ইচ্ছে পাঠাও খবর নিতে। যেখানে ইচ্ছে, যতদিন ইচ্ছে থাকতে হয়, থাকুক। যত খরচ হয় হোক। কোনও অসুবিধে নেই। কিন্তু খবর চাই। পাকা খবর। যে-কোনও মূল্যে।
চারটে ‘জোন’-এ ভাগ করে নেওয়া হয়েছিল কলকাতা সংলগ্ন জেলাগুলোকে। হাওড়া, হুগলি, উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা। দশ-বারো জন সোর্সকে থাকা-খাওয়ার খরচ দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল প্রতিটি জোনে। সোর্সদের কাজকর্মের তত্ত্বাবধানে প্রতি টিমের সঙ্গে ছিলেন গোয়েন্দাবিভাগের অন্তত দু’জন অফিসার।
পাঁচ তদন্তকারী অফিসার, ইন্দ্রনীল-তরুণ-রাম-তপন-শাকিলুর সারা সপ্তাহ ধরে জেলাগুলোয় চক্কর দিয়ে বেড়াতেন। রোজ কথা বলতেন ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকা সোর্স এবং অফিসারদের সঙ্গে।
এতটাই মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন তদন্তকারীরা, সোর্সের দেওয়া খবরের গুণাগুণ বিচারের বিলাসিতা ছিল না। সেই বিশেষ টিমের একজনের ভাষায়, ‘নাওয়াখাওয়া ভুলতে বসার অবস্থা হয়েছিল আমাদের। যে সোর্স যখন যা বলছে, অন্ধের মতো ছুটছি তখন। ক্লু হাতে না থাকলে যা হয়। কেউ বলল, নৈহাটির শিবদাসপুরে নাকি কয়েকটা ছেলে প্রচুর টাকা ওড়াচ্ছে। ছুটলাম নৈহাটি। পরের দিনই খবর এল হয়তো, আন্দুলে একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে কয়েক মাস ধরে সাত-আটজন লোক রয়েছে। সকালে বেরিয়ে যায়, রাতে ফেরে। কেউ জানে না কী করে ওরা। ব্যস, ছোটো আন্দুল। কিন্তু কোনও খবরই “ক্লিক” করছিল না।’
‘ক্লিক’ করার সামান্য আভাস মিলল ’৯৮-এর জানুয়ারির মাঝামাঝি। প্রথম ডাকাতির পর প্রায় ছ’মাস অতিক্রান্ত তখন। মিনাখাঁয় একজন সোর্স কিছু খবর দিয়েছিল। সেই খবর যাচাই করতে আমিনুল হক সহ পাঁচ তদন্তকারী একটা পরিত্যক্ত বাড়িতে রেইড করে ফিরছিলেন কলকাতায়। নিষ্ফলা রেইড। খবরটা ভুল ছিল।
গাড়ি ছুটছিল বাসন্তী হাইওয়ে দিয়ে। বেশ কিছুক্ষণ হল ভোর হয়ে গেছে। শীতের ভোর। অফিসারদের সোয়েটার-শাল-জ্যাকেটকে বলে বলে গোল দিচ্ছে ফাঁকা হাইওয়ের উত্তুরে হাওয়া।
রাস্তার ধারের দু’-একটা চায়ের দোকান ঝাঁপ খুলেছে। ভোজেরহাটের এমনই একটা দোকানের সামনে গাড়ি ব্রেক কষল। অফিসাররা সিদ্ধান্ত নিলেন, একটু চা না হলেই নয়। ঘুমটা তো অন্তত কাটুক। হাড়-কাঁপানো ঠান্ডাটাও।
ভাঁড়ের চা, ধোঁওয়া-ওঠা। আয়েশি চুমুক দিতে দিতেই আমিনুল এবং বাকিরা লক্ষ করলেন, অন্তত পনেরো-কুড়িটা ট্রাক সার দিয়ে চলেছে বাসন্তীর দিকে। সবক’টা ইটবোঝাই। এ রাস্তায় তো এত ইটভাটা নেই! ইটভরতি ডজনখানেক ট্রাক যাচ্ছে কোথায়? কোনও ব্রেনওয়েভ নয়। কোনও মগজাস্ত্র নয়। নিছকই কৌতূহলে আমিনুল প্রশ্ন করেন চায়ের দোকানিকে।
—এতগুলো ট্রাক! সব কি ইটভাটায় যায়? এ রাস্তায় এত ইটভাটা আছে?
—না স্যার, ইটভাটা নয়। আকুঞ্জি মার্কেট তৈরি হচ্ছে তো ধামাখালিতে। ওখানে যাচ্ছে। রোজই এ সময় যায়। ইট যায়। সিমেন্ট যায়। বালি যায়।
—কী মার্কেট?
—আকুঞ্জি। আকুঞ্জি মার্কেট।
.
‘যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই’—তদন্তের চিরন্তন আপ্তবাক্য। ছাই উড়িয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। যোগাযোগ করা হল ধামাখালির দু’জন সোর্সের সঙ্গে, ‘খবর চাই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। কোথায় মার্কেট তৈরি হচ্ছে, কারা করছে, কত টাকা খরচ হচ্ছে, সব খবর চাই।’
চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই খবর এল। ধামাখালির আকুঞ্জিপাড়ায় সবাই একডাকে চেনে আকুঞ্জি পরিবারকে। বিঘের পর বিঘের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে মাছের ভেড়ির মালিক এই আকুঞ্জিরা। গলদা চিংড়ির রপ্তানিই প্রধান ব্যবসা। চাষবাসের জমিজমাও আছে যথেষ্ট। তবে ভেড়িই রোজগারের মূল উৎস। প্রচুর স্থানীয় লোক কাজ করে আকুঞ্জিদের ভেড়িতে। এলাকার অন্যতম সম্পন্ন পরিবার।
মাসখানেক আগে হাইওয়ে সংলগ্ন এলাকায় শুরু হয়েছে আকুঞ্জি মার্কেট তৈরির কাজ। বিশাল এলাকা জুড়ে বসবে বাজার। একটা বড় বাজারের দীর্ঘদিনের অভাব স্থানীয় মানুষের। সেই অভাব দূর করতে উদ্যোগী হয়েছে আকুঞ্জিরা। কাজ চলছে ঝড়ের গতিতে। ইট-বালি-চুন-সুরকি বোঝাই গাড়ির দাপাদাপি লেগেই আছে।
শুধু বাজারই নয়, মাসদেড়েক হল পাড়ায় একটা মসজিদও তৈরি করে দিয়েছে আকুঞ্জিরা। নামাজ পড়তে কয়েক কিলোমিটার হেঁটে দূরের মসজিদে যেতে হত এর আগে। অসুবিধে হত বয়স্কদের। এখন পাড়ার মধ্যেই প্রার্থনার সুব্যবস্থা। সৌজন্য, আকুঞ্জি পরিবার।
যথেষ্ট ধনী পরিবার ঠিকই। কিন্তু হঠাৎ করে এত টাকা আসছে কোত্থেকে, যে রাতারাতি মসজিদ বানানো হয়ে গেল, বাজারও তৈরি হওয়ার মুখে? ভেড়ির কর্মচারীদের কাছে খোঁজ নিয়ে সোর্স জানাল, ব্যবসা চলছে আগের মতোই। মাছ রপ্তানির পরিমাণ যে হঠাৎ বেড়েছে, এমন নয়। তা হলে?
আকুঞ্জি পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হল বিস্তারিত। এবং যা জানা গেল, তাতে ‘সামান্য আলোর আভাস’ দেখতে পেলেন গোয়েন্দারা, দীর্ঘদিন ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ধুঁকতে থাকার পর রোগী জেনারেল বেডে ফেরার ছাড়পত্র পেলে যেমন হয়।
পরিবারের মাথা হলেন মধ্যপঞ্চাশের আবদুল কাদের আকুঞ্জি। চার ছেলে। বড়ছেলের বয়স তিরিশ, নাম আবদুল মাজেদ আকুঞ্জি। মেজোছেলে আঠাশ, নাম আবদুল ওয়াজেদ। সেজোর বয়স হয়েছে চব্বিশ-পঁচিশ, আবদুল ওয়াহেদ। ছোটছেলে স্কুলে পড়ে, আবদুল ওহিদ।
ছোটছেলেকে হিসেবের বাইরে রাখা হল। মাজেদ-ওয়াজেদ-ওয়াহেদ, বড়-মেজো-সেজো-র গতিবিধি কেমন?
জানা গেল, বড় এবং সেজো ভেড়ির কাজেই সাহায্য করে বাবাকে। মেজোছেলে, ওয়াজেদ আকুঞ্জি, নিয়মিত যাতায়াত করে কলকাতায়, ব্যবসার কাজে। কখনও মোটরসাইকেলে করে, কখনও পারিবারিক গাড়িতে। বেশিরভাগ সময়েই কলকাতাতেই থাকে ইদানীং। গত কয়েক মাস পাড়ার লোক খুব বেশি হলে
দু’-তিনবার এলাকায় দেখেছেন ওয়াজেদকে।
পাঁচটা ডাকাতিতে প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী আঁকা ছয় ডাকাতের ছবি দেখানো হল স্থানীয় কয়েকজনকে। একটা ছবিকে প্রায় সবাই চিহ্নিত করলেন, ‘আরে! এ তো একদম ওয়াজেদ ভাইয়ের মতো দেখতে।’
ছবি দেখে লোকে চিনছে। হঠাৎ টাকা খরচ হচ্ছে জলের মতো। পরিবারের তরফে রাতারাতি এলাকায় তৈরি হচ্ছে মসজিদ। গড়ে উঠছে বাজার। কলকাতায় মেজোছেলে ওয়াজেদ পুরো মাসটাই কাটাচ্ছে। দেখাই যাচ্ছে না এলাকায়। এই পরিস্থিতিতে লালমোহনবাবু হলে যা বলতেন, সেটাই মাথায় ঘুরছিল গোয়েন্দাদের। ‘হাইলি সাসপিশাস!’
সব দিক বিচার করে একটাই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ছিল। আকুঞ্জিদের বাড়িতে ‘রেইড’ করার।
.
প্রায় তিন বিঘে জমির উপর বাড়ি। বাড়ি তো নয়, যেন দুর্গ। দশ-বারো ফুট উঁচু পাঁচিল। ঢোকার গেট একটাই। পুরো বাড়িটা ঘিরে ফেলতে পঞ্চাশ-ষাট জন লোকের দরকার ন্যূনতম।
সামান্যতম ঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত ছিল না লালবাজার। একশো জন বাছাই করা পুলিশকর্মীকে জড়ো করা হয়েছিল ধামাখালিতে। হাজির ছিলেন আমিনুলের নেতৃত্বে অন্তত ডজনখানেক অফিসার। ঘড়ির কাঁটা যখন রাত তিনটে ছুঁতে চলেছে, আকুঞ্জিদের বাড়ির দরজায় কড়া নাড়া হল। জবাব এল না।
আগের রাত্রে সাদা পোশাকে কয়েকজন অফিসার ঘুরে গিয়েছিলেন জায়গাটা। একটা বড় ‘রেইড’ করার আগে সরেজমিনে যে ‘ঘুরে যাওয়াটা’ অসম্ভব জরুরি। কোথায় ‘রেইড’ হবে, কোন দিক দিয়ে ঢোকা হবে, ভিতরে কারা যাবে, বাইরে ‘ব্যাক-আপ’ হিসাবে কারা থাকবে, যাদের ধরতে যাওয়া হচ্ছে, তারা কোনদিক দিয়ে পালাতে পারে, এবং সেই পালানোর পথ কীভাবে বন্ধ করতে হবে… সমস্ত খুঁটিনাটি ছবি এঁকে আগেভাগে বুঝিয়ে দেওয়া হয় ‘রেইড’-এ অংশ নেওয়া অফিসার-কর্মীদের। কার কখন কী দায়িত্ব, পরিষ্কার হয়ে যায় জলবৎ তরলং।
কড়া নেড়েও জবাব না এলে কী করা হবে, ভাবাই ছিল। আনা হয়েছিল বেশ কয়েকটা কাঠের সিঁড়ি। লাগানো হল পাঁচিলের গায়ে। জনা কুড়ি অফিসার-ফোর্স সিঁড়ি বেয়ে উঠে পাঁচিল টপকে নেমে পড়লেন বাড়ির ভিতরে। গেট খুলে দিলেন বাড়ির। বাকি ফোর্স ঢুকে পড়ল। প্রত্যেকের হাতে হয় টর্চ, নয় ড্রাগন লাইট।
তিন বিঘে জমির উপর যেন একটুকরো গ্রাম। ছোট ছোট আটটা ঘর ছড়িয়ে ছিটিয়ে। একটা পুকুর। গোরু-বাছুর বাঁধা রয়েছে একটা বড় গোয়ালঘরে। এক প্রান্তে দুটো গুদামঘর। ধান বোঝাই করা আছে। ধানের স্তূপ অবশ্য শুধু গুদামেই নয়, সাজানো রয়েছে বিস্তৃত জমির এখানে-ওখানে-সেখানে।
পুকুরের ঠিক পাশেই অন্যগুলোর তুলনায় একটু বড় একটা ঘর। যার কড়া নাড়তে দরজা খুলে ঘুমচোখে বেরিয়ে এলেন পরিবারের কর্তা। আবদুল কাদের আকুঞ্জি। শক্তপোক্ত চেহারা। ফতুয়া-লুঙ্গি পরিহিত ভদ্রলোক পুলিশ দেখে অবাক। শান্ত গলায় প্রশ্ন করলেন আমিনুলকে।
—কী ব্যাপার? আপনারা এভাবে সবাই মিলে আমার বাড়িতে… কী ব্যাপার?
—বলছি… আপনার ছেলেদের ডাকুন। আমরা লালবাজার থেকে আসছি। আপনার বাড়িটা সার্চ করব।
এবার সামান্য উত্তেজিত দেখায় সিনিয়র আকুঞ্জিকে।
—সার্চ করবেন মানে? কী সার্চ করবেন? আমরা কি চোর-ডাকাত নাকি? সার্চ ওয়ারেন্ট কোথায়? সার্চ করবেন বললেই হল? দেশে আইন নেই?
—আইনের আলোচনা আপনার সঙ্গে করতে আসিনি আকুঞ্জি সাহেব। আর চোর-ডাকাত কিনা সেটা তো আপনি ভাল বলতে পারবেন… আপনার ছেলেরা বলতে পারবে… কোথায় ওরা?
‘কোথায়’, সেটা জানতে ততক্ষণে আকুঞ্জিদের বাড়ির প্রতিটি কোনায় তল্লাশি শুরু করে দিয়েছে পুলিশবাহিনী। গুদামঘর-গোয়ালঘর-ধানের স্তূপ, কিছু বাদ নেই। কয়েকটা ঘর তালাবন্ধ ছিল। বাকিগুলো থেকে বেরিয়ে এসেছেন পরিবারের অন্য সদস্যরা। বেরিয়ে এসেছেন বাড়ির কাজের লোকরাও।
পুরুষ সদস্য বলতে গৃহকর্তা নিজে ছাড়াও উপস্থিত চার ছেলের মধ্যে তিনজন।বড় মাজেদ, সেজো ওয়াহেদ এবং স্কুলপড়ুয়া ছোটছেলে ওহিদ।
—আপনার মেজোছেলে ওয়াজেদ কই?
—ও বেশিরভাগ সময় ব্যবসার কাজে কলকাতায় থাকে। মাসে এক-দু’দিন আসে।
—কোথায় থাকে কলকাতায়?
—সেটা বলতে পারব না।
—শেষ কবে এসেছিল এখানে?
—মাসখানেক আগে হবে।
—ভালই তো ব্যবসা আপনাদের, ডাকাতির মধ্যে না ঢুকলে চলছিল না?
এবার রাগে ফেটে পড়েন আকুঞ্জি সাহেব।
—মানে? বাড়ি বয়ে এসে যা খুশি বলবেন, যা খুশি করবেন? স্রেফ পুলিশ বলে? কে ডাকাতি করেছে? এপাড়ায় কতদিন ধরে আছি জানেন? খোঁজ নিয়ে দেখুন না আমাদের ব্যাপারে! পুরো বাড়ি তছনছ করে দিচ্ছেন সার্চের নামে, আমি আপনাদের ছেড়ে দেব ভেবেছেন? কোর্টে যাব।
কোর্টে যাওয়ার সত্যিই সংগত কারণ থাকবে, অফিসাররা বুঝতে পারছিলেন তল্লাশির পর। কিছুই পাওয়া গেল না তন্নতন্ন করে খোঁজার পরও। রিভলভার না, গুলি না, বোমা না। ব্যাংকলুঠের একটা টাকাও না।
হাল ছেড়ে দেওয়ার প্রশ্ন ছিল না। সিনিয়র আকুঞ্জির প্রবল প্রতিবাদকে উপেক্ষা করেই জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গোয়েন্দারা লালবাজারে নিয়ে এলেন মাজেদ আর ওয়াহেদকে।
নিয়ে তো এলেন। কিন্তু রাতভর ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা করেও ডাকাতির ব্যাপারে স্বীকারোক্তি তো দূরের কথা, কোনও বাড়তি তথ্যও পাওয়া গেল না। দু’জনেই একই কথা আউড়ে গেলেন তোতাপাখির মতো, ‘ডাকাতির ব্যাপারে কিছুই জানি না আমরা।’
মেজোভাই ওয়াজেদ কোথায়? দুই ভাইয়ের একই উত্তর কাটা রেকর্ডকেও লজ্জা দিয়ে, ‘বিশ্বাস করুন, জানি না।’ গ্রেফতারির প্রশ্ন আসে অপরাধের সঙ্গে নির্দিষ্ট যোগসূত্র বা প্রমাণ পাওয়া গেলে তবেই। পাওয়া গেল না, এবং ছেড়ে দিতে হল দুই ভাইকে। সোর্সদের বলা হল গতিবিধির উপর নজর রাখতে।
নজরদারির ব্যাপারে একটা জরুরি সিদ্ধান্ত নিলেন গোয়েন্দাপ্রধান। হাওড়া-হুগলি-উত্তর ২৪ পরগনায় যে অফিসাররা ঘাঁটি গেড়েছিলেন সোর্সসহ, তাদের সবাইকে বলা হল দক্ষিণ ২৪ পরগনায় চলে আসতে। বামনঘাটা-ভোজেরহাট-ঘটকপুকুর-মিনাখাঁ-মালঞ্চ হয়ে ধামাখালি পর্যন্ত, সর্বত্র ছড়িয়ে গেলেন অফিসাররা। বৃত্তটা ছোট হয়ে এল অনেক। এলাকায় পাকাপাকি নোঙর ফেলে খবর জোগাড়ের চেষ্টা শুরু করল সোর্সরা। ওয়াজেদ আকুঞ্জি কোথায়?
খবর এল। দ্রুতই এল। ওয়াজেদ আকুঞ্জিকে সপ্তাহখানেক আগে দেখা গেছে ঘটকপুকুর এলাকায়। হাইওয়ের ধারে একটা চায়ের দোকানে সন্ধেবেলা এসেছিল মিনিট দশেকের জন্য। একজন লোকের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে চলে গেছে মোটরসাইকেলে করে। দোকানির সঙ্গে কথা বললেন গোয়েন্দারা।
—লোকটা কার সঙ্গে কথা বলছিল চায়ের দোকানে?
—একটা বেঁটে মতো লোক, মোটাসোটা।
এই সেই ‘দুয়ে দুয়ে চার’-এর মুহূর্ত! বেঁটে মতো লোক? মোটাসোটা? Hefty and bulky? যেমনটা এফআইআর-এ লিখেছিলেন ফেডারাল ব্যাংকের ম্যানেজার রামচন্দ্রন? ঠিক যেমন চেহারার লোকের বিবরণ পাওয়া গেছে পাঁচটা ঘটনাতেই?
—চেনেন ওই বেঁটে লোকটাকে?
—এক-দু’বার এসেছে আমার এখানে চা খেতে। মুখ চিনি। নাম জানি না।
—হুঁ… বেঁটে লোকটা যার সঙ্গে কথা বলছিল, সে একা এসেছিল?
—না স্যার, সঙ্গে একটা মেয়ে ছিল।
—মেয়ে?
—হ্যাঁ স্যার, কুড়ি-বাইশ বছর বয়স হবে। খুব ফরসা। লম্বা। দারুণ দেখতে।
—মেয়েটিকে আগে এলাকায় দেখেছেন কখনও?
—না স্যার… আমি বরং লোকটা মেয়েটাকে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে বেরিয়ে যাওয়ার পর ওই বেঁটে মোটা লোকটাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, একে তো আগে দেখিনি কখনও এদিকে?
—কী বলেছিল?
—বলেছিল, মেয়েটা নাকি নাচে। কলকাতায়।
পরের চব্বিশ ঘণ্টায় ঘটকপুকুর এবং সংলগ্ন এলাকার গ্রামগুলো সাদা পোশাকের পুলিশ এবং সোর্সরা চষে ফেলল। এবং জানা গেল ‘hefty and bulky’ লোকটির পরিচয়। আবদুল হাই গায়েন। বড়ালি গ্রামের বাসিন্দা। ইটভাটার মালিক। কলকাতায় চালের ব্যবসা করত একসময়। লরি চালাতে পারে। এলাকায় যথেষ্ট দাপট। ইটভাটার লরি পার্ক করা নিয়ে সম্প্রতি স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছিল। হাতাহাতিও। আবদুল হাই নাকি শূন্যে গুলি চালিয়েছিল ঝামেলার সময়। বছর দুয়েক আগে চুরি-ছিনতাই জাতীয় কেসে নাকি একবার পুলিশে ধরাও পড়েছিল। ইদানীং বাড়িতে থাকছে না।
সন্দেহের-দ্বিধার-সংশয়ের আর জায়গা ছিল না। ছয় ডাকাতের দু’জন নিশ্চিতভাবে আকুঞ্জি এবং আবদুল হাই। এদের ধরতে পারলেই বাকি চারের হদিশ মিলবে।
কীভাবে ধরা হবে? হাতের কাছে তথ্য বলতে, আকুঞ্জিকে একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা গেছে। কলকাতায় নাচে। কোথায় নাচে? নিশ্চয়ই পানশালায়, কোনও বারে।
কলকাতার বারে নাচে, এমন একটা মেয়েকে খুঁজে বার করতে হবে। লম্বা-ফরসা-সুন্দরী। যার সঙ্গে ধামাখালির এক যুবকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়েছে ইদানীং। এটুকু না পারলে আর কীসের লালবাজার? কীসের আর স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে তুলনা?
দু’জন সোর্সকে চিহ্নিত করা হল। যাদের নিয়মিত যাতায়াত আছে কলকাতার সেইসব পানশালায়, যেখানে গানের পাশাপাশি টুকটাক নাচও হয়। বলে দেওয়া হল, ‘সন্ধে থেকে বারগুলোতেই কাটাও। যা খরচা হবে, আমরা দেব।’
দিনতিনেকের মধ্যেই খবর নিয়ে হাজির হল সোর্স। আসল নামটা লিখলাম না। নাম ধরা যাক আশিস। নিখরচায় সন্ধে থেকে ‘জলপথে’ থাকার সুযোগ পেয়ে যে জানপ্রাণ লাগিয়ে দিয়েছিল মেয়েটিকে খুঁজে বার করতে।
—স্যার। ইলিয়ট রোডের কাছে বারটা। মেয়েটা হাতিবাগানের।
—কী করে বুঝলি, এই মেয়েটাই?
অঙ্কে এমএসসি করা লোককে যদি জিজ্ঞেস করেন এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের ফরমুলা? কী প্রতিক্রিয়া হবে? অনুকম্পার হাসিই তো! অবিকল সেই হাসি হাসলেন আশিস।
—কী যে বলেন স্যার! এটা বোঝা কোনও ব্যাপার হল? বারে নাচে, ফরসা-লম্বা আর সুন্দর দেখতে, এমন পাঁচটা মেয়ের খোঁজ পেলাম গত দু’দিনে। লোক ফিট করলাম পাঁচজনের পিছনে। এই হাতিবাগানের মেয়েটা কিছুদিন হল ট্যাক্সি করে বারে আসছে। আগে বাসে করে আসত। গলায় মাসখানেক হল সোনার নেকলেস পরছে। হেব্বি দামি ঘড়ি পরছে।
—আর?
—গত শনিবার একটা গাড়ি এসে বারের বাইরে অপেক্ষা করছিল। নাচ শেষ হওয়ার পর সেই গাড়িতে করে মেয়েটা বেরিয়ে গেছে। একটা ছেলে গাড়িটা চালাচ্ছিল। ছেলেটার ব্যাপারে তেমন কেউ বলতে পারছে না। তবে মেয়েটার চালচলন ইদানীং বদলে গেছে। হাতে মালকড়ি এসেছে হঠাৎ। আমি হাতিবাগানেও খোঁজ নিয়েছি। বাড়ির অবস্থা ভাল নয় তেমন টাকাপয়সার দিক দিয়ে। আপনি মিলিয়ে নেবেন স্যার, একেই খুঁজছেন। এই মেয়েটাই!
.
শেষ-জানুয়ারির শনিবারের রাত। লালবাজার থেকে প্লেন ড্রেসে রওনা দিলেন গোয়েন্দারা। ইলিয়ট রোডের বারের বাইরে অপেক্ষায় রইলেন বিমল-আমিনুল-রাম-তপনরা। সঙ্গে দুই মহিলা কনস্টেবল। ভিতরে ঢুকলেন রিমলেস চশমা পরিহিত ইন্দ্রনীল। বার তখন মাতোয়ারা। হিট হিন্দি গানের সঙ্গে কোমর দোলাচ্ছেন এক সুন্দরী। লম্বা এবং ফরসা।
‘তু চিজ বড়ি হ্যায় মস্ত মস্ত
তু চিজ বড়ি হ্যায় মস্ত..’
গানের মাঝেই ম্যানেজারের কানে ইন্দ্রনীলের ফিসফিস। গান শেষ হওয়ার পরই তরুণীর শশব্যস্ত বেরিয়ে আসা বারের বাইরে।
—আপনাকে একবার আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।
—যেতে হবে মানে? কোথা থেকে আসছেন আপনারা?
—লালবাজার।
ড্রেস চেঞ্জ করতে যতটুকু সময়। সাদা টাটা সুমো গাড়িতে উঠে বসলেন তরুণী। টাটা সুমো স্টার্ট দিল। গন্তব্য লালবাজার।
পানশালার মেহফিলে তখন যুবতীর জায়গা নিয়েছে এক যুবক। শুরু হয়েছে নতুন গান। শাহরুখ খানের সিনেমার।
‘ইয়ে কালি কালি আঁখে
ইয়ে গোরে গোরে গাল…’
.
একটা মাঝারি মাপের ঘরে সাত-আটজন মিলে জেরা করতে শুরু করলেন যুবতীকে। এবং মিনিট পাঁচেকের বেশি নার্ভ ধরে রাখতে পারলেন না যুবতী। ওঁর আসল নামটা বদলে দেওয়া যাক। ধরা যাক, জয়শ্রী। স্বীকার করে নিলেন আকুঞ্জির সঙ্গে গড়ে ওঠা মাসদুয়েকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সম্পর্কের কী-কেন-কখন নিয়ে বিশেষ কৌতূহল ছিল না অফিসারদের। জানার ছিল একটা কথাই। কলকাতায় আকুঞ্জি থাকে কোথায়? উত্তর দেবেন কী, প্রশ্ন শোনামাত্রই হাউহাউ করে কেঁদে ফেললেন জয়শ্রী।
—স্যার, জানতে পারলে ও মেরে ফেলবে আমাকে। সবসময় সঙ্গে রিভলভার থাকে ওর। সংসারটা আমাকে একা চালাতে হয়। মাসে মাসে চার হাজার করে টাকা দিত আমায়। সেই লোভে পড়ে… প্লিজ় স্যার, ও আমায় মেরে ফেলবে জানতে পারলে…
অফিসাররা নানাভাবে আশ্বস্ত করেন জয়শ্রীকে।
—কেউ জানবে না আপনার নাম। কেস ডায়েরিতে কোথাও থাকবে না। কোর্টে যেতে হবে না। কিস্যু করতে হবে না। কথা দিচ্ছি আমরা। বারের ম্যানেজারকে বলে দেব আমরা। আপনি শুধু জায়গাটা দেখিয়ে দেবেন, ব্যস। বললে আপনারই সুবিধে, ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখুন। না বললেই বরং ফাঁসবেন।
আধঘণ্টা পর ধাতস্থ হলেন জয়শ্রী। যতটুকু জানতেন, বললেন। রাত আড়াইটে নাগাদ জয়শ্রীকে সঙ্গে নিয়ে চারটে অ্যামবাসাডর গাড়ি বেরল লালবাজার থেকে। প্রথম দুটো গাড়িতে জয়শ্রীকে বাদ দিয়ে আরোহীর সংখ্যা আট। প্রত্যেকে সাদা পোশাকে। কোমরে গোঁজা .৩২ রিভলভার। লোডেড। সঙ্গে একটা ব্যাগ। যাতে রইল শাবল-গাঁইতি।
তিন নম্বর গাড়িতে দু’জন মহিলা কনস্টেবল এবং একজন অফিসার। চতুর্থ গাড়িতে চার উর্দিধারী, বন্দুকসহ।
রবীন্দ্র সরণি-পোদ্দার কোর্ট-চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-গিরিশ পার্ক-বিবেকানন্দ রোড-কাঁকুড়গাছি-উলটোডাঙা হয়ে চারটে গাড়ির প্রথম দুটো ঢুকে পড়ল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এলাকায়। কিছুটা এগিয়ে বাঁক নিল বাঁ দিকে। তিন আর চার নম্বর গাড়ি থেকে গেল উলটোডাঙা মোড়ে।
প্রথম দুটো গাড়িও থামল একটু পরেই। লেকটাউনের কালিন্দী হাউসিং প্রোজেক্ট থেকে একটু দূরে। একতলায় একটা ফ্ল্যাটের সামনে অফিসারদের নিয়ে গেলেন জয়শ্রী। ওঁর কাজ শেষ। পৌঁছে দেওয়া হল উলটোডাঙায়। যেখানে অপেক্ষমাণ তিন নম্বর গাড়িতে করে দু’জন অফিসার এবং একজন মহিলা কনস্টেবল জয়শ্রীকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন হাতিবাগানের বাড়িতে পৌঁছে দিতে।
দরজার দু’দিকে ভাগ হয়ে গেলেন অফিসাররা। পাঁচ তদন্তকারী ছাড়াও দলে ছিলেন সাব-ইনস্পেকটর মনোজ দাস এবং আরও দুই অফিসার। তাগড়াই চেহারার মনোজ (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ডেপুটেশনে ডিএসপি হিসাবে কর্মরত) কলকাতা পুলিশে ডাকাবুকো অফিসার বলে পরিচিত ছিলেন।
প্রথমবারের কড়া নাড়ায় কোনও আওয়াজ নেই ঘরের ভিতর থেকে। দ্বিতীয়বারে ছিটকে এল মরিয়া উত্তর,— ‘পুলিশ হোক আর যেই হোক, ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করলেই গুলি করব।’
লাথি মেরে দরজা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে ছিটকে এল গুলি। লাগল মনোজের কাঁধে। অবিরাম রক্তপাত, ক্ষতস্থানে হাত চেপে মাটিতে বসে পড়লেন মনোজ। এবং ঘরের ভিতর থেকে দ্বিতীয় গুলি চলার আগেই পালটা গুলি চালালেন এক অফিসার। আকুঞ্জির কোমরের নীচে, ডান ঊরুর কাছে গুলি লাগল। এ-ই যে আকুঞ্জি, এক পলকের দেখাতেই বুঝলেন গোয়েন্দারা। আঁকানো ছবির সঙ্গে যথেষ্টরও বেশি মিল।
আকুঞ্জি একা ছিল না ফ্ল্যাটে। সঙ্গে ছিল আরেকজন। দু’জনের উপরই নিমেষে ঝাঁপালেন গোয়েন্দারা। কেড়ে নেওয়া হল আকুঞ্জির রিভলভার। অন্য লোকটিকে ধরাশায়ী করতেও লাগল খুব বেশি হলে পনেরো সেকেন্ড। ওয়াকিটকিতে ততক্ষণে খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন এক অফিসার, ‘মুভ টু কালিন্দী অ্যাট ওয়ান্স। কুইক!’ উলটোডাঙার মোড় থেকে চতুর্থ গাড়ি তখন তিরবেগে ছুটেছে লেকটাউনের দিকে।
গুলিগোলার আওয়াজে তখন ঘুম ভেঙে গেছে আশেপাশের বাসিন্দাদের। আতঙ্কে অনেকে বেরিয়ে এসেছেন রাস্তায়। এবং বিস্ফারিত চোখে দেখছেন, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় এক অফিসারকে ধরাধরি করে অ্যাম্বুলেন্সে তুলছেন সতীর্থরা। দুই যুবককে একতলার ফ্ল্যাট থেকে টেনে বার করে আনছে পুলিশ। একজনের কোমরে দড়ি। আর একজন রক্তাক্ত। তাকেও তোলা হচ্ছে অ্যাম্বুলেন্সে। আরে, এ তো চেনা মুখ। ভদ্র, নম্র ব্যবহার। মাসছয়েক হল এখানে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছে। প্রোমোটারি করে বলেই জানে পাড়ার লোক। এ? এ ব্যাংক-ডাকাতির পান্ডা!
আহত মনোজ এবং ওয়াজেদ আকুঞ্জিকে নিয়ে যাওয়া হল আর জি কর হাসপাতালে। কালিন্দীর ফ্ল্যাট তল্লাশি করে পাওয়া গেল দুই আলমারি ভরতি টাকা। থরে থরে সাজানো, বিভিন্ন ব্যাংকের স্লিপ লাগানো টাকার বান্ডিল।
আকুঞ্জির সঙ্গের যুবকের নাম মনোজ সিং। যাকে লালবাজারে এনে শুরু হল জিজ্ঞাসাবাদ। সব কিছু স্বীকার করা ছাড়া উপায় ছিল না ট্যাংরার দেবেন্দ্র চন্দ্র রোডের বাসিন্দা মনোজের। দ্রুত জানিয়ে দিল ডাকাতদলের বাকিদের নাম। ভোরেই বেরিয়ে পড়া হল রেইডে। সমর রায় ওরফে কালু গ্রেফতার হল ট্যাংরা থেকেই। কড়েয়ার একটা ভাড়াবাড়ি থেকে তোলা হল আরেক ডাকাত দীনেশ দাসকে। এন্টালির বিবিবাগানের গোপন ডেরায় হানা দিয়ে গ্রেফতার করা হল সরওয়ার খানকে। মনোজ-দীনেশ-সমর-সরওয়ার, সবারই বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে।
সমর-দীনেশরা জানত ঘটকপুকুরের কাছে আবদুল হাই গায়েনের সম্ভাব্য আস্তানার কথা। টিম পাঠিয়ে ডাকাতদলের একমাত্র ‘hefty and bulky’ সদস্যকে পাকড়াও করতে সমস্যা হওয়ার কথা ছিল না। হলও না। আকুঞ্জি-মনোজ-আবদুল-সরওয়ার-দীনেশ-সমর, পুরো গ্যাং শেষ পর্যন্ত কব্জায়। প্রথম ডাকাতির প্রায় ছ’মাস পরে।
কোথায় কখন ডাকাতি করা হবে, প্ল্যান করত দু’জন। আকুঞ্জিই ছিল দলের মাথা। সংলাপ-চিত্রনাট্য-পরিচালনা তারই। মুখ্য পরামর্শদাতা ছিল আবদুল, যার সঙ্গে আকুঞ্জির আলাপ বেশ কয়েক বছর আগে। আবদুলের আর্থিক টানাটানির সময় আকুঞ্জি টাকাপয়সা দিয়ে বিস্তর সাহায্য করেছিল। সেই থেকেই আবদুল আপাদমস্তক অনুগত আকুঞ্জির প্রতি।
পঁয়ত্রিশ বছরের আবদুল কলকাতার রাস্তাঘাট, অলিগলি চিনত হাতের তালুর মতো। প্রায় পাঁচ বছর বড়বাজারের একটা চাল ব্যবসায়ীর কাছে কাজ করেছে। লরি চালিয়ে চাল নিয়ে গেছে শহরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা। কোথায় কখন কীভাবে হানা দিলে দ্রুত কাজ হাসিল হবে আর পালানোও যাবে নিরাপদে, আবদুলই বুদ্ধি দিত আকুঞ্জিকে। এবং আবদুলই পুরনো পরিচয়ের সূত্রে জুটিয়েছিল টিমের বাকি চারজনকে। মনোজ-সমর ট্যাংরায় একই পাড়ার বাসিন্দা। কাঠবেকার দু’জনেই। দীনেশ এবং সরওয়ারেরও কাজকর্ম বিশেষ কিছু ছিল না। পাড়ায় খুচরো দাদাগিরির ইতিহাস ছিল কিছু।
যেখানে যেখানে ডাকাতি হয়েছিল, সেখানে তার আগের রাতে পুরো টিমকে নিয়ে হাজির হত আকুঞ্জি। জায়গাটা আরও আগে থেকে দেখে রাখত আবদুল। ডাকাতির পর যে রাস্তা দিয়ে চম্পট দিতে হবে, সেই রাস্তা দিয়ে এরা ‘ট্রায়াল রান’ দিত গভীর রাতে। পরের দিন যাতে কোনও বিভ্রান্তি না থাকে, পান থেকে যাতে চুন না খসে।
যে মোটরসাইকেলগুলো ব্যবহার হয়েছিল ডাকাতিতে, সবক’টাই চোরাই। জোগাড় করেছিল আবদুলই। ট্যাংরার ডাকাতিতে ব্যবহৃত হয়েছিল যে মারুতি গাড়ি, সেটাও চোরাই গাড়িই। খোঁজ মিলল না গাড়িগুলোর। আকুঞ্জিরই পরামর্শমতো মোটরসাইকেল দুটো আবদুল ধাপার মাঠের কাছে ফেলে দিয়ে এসেছিল পাঁচ নম্বর ডাকাতির পর। সেগুলো খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। পাওয়া গেলও না।
মারুতি গাড়িটা? বসিরহাটের টাকির বাসিন্দা এক পরিচিতের কাছ থেকে কয়েকদিনের জন্য গাড়িটা ধার নিয়েছিল আবদুল। যাওয়া হল সেই পরিচিতের বাড়ি। তালাচাবি বন্ধ করে মাসখানেক আগে বাড়ির বাসিন্দারা অন্য কোথাও চলে গিয়েছেন।
আহত সাব-ইনস্পেকটর মনোজ সুস্থ হয়ে উঠলেন ক্রমশ। মাসখানেক পরে পুলিশি প্রহরায় চিকিৎসাধীন আকুঞ্জিও সুস্থ হয়ে উঠল। লালবাজারে জেরার মুখোমুখি হয়ে আকুঞ্জি প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর দিল সোজাসাপটা। বুঝে গিয়েছিল, ‘গেম ওভার’। কিছু লুকিয়ে আর লাভ নেই। বাকিরা সবটা বলে দিয়েছে। মিথ্যে বললে দুর্ভোগই বাড়বে। পুলিশ বিশ্বরূপ দেখিয়ে ছাড়বে।
—এত জমিজমা, মাছের এমন রমরমা ব্যবসা, নতুন গ্যাং তৈরি করে ডাকাতির প্ল্যান কী করে মাথায় এল? আর কেনই বা এল?
জবাবে আকুঞ্জি কোনও রাখঢাক করল না।
—ফ্যামিলি বিজ়নেসেই থাকলে যেমন চলছিল, তেমনই চলত স্যার। আমার আরও আরও অনেক বেশি বড়লোক হওয়ার ইচ্ছে হত। বিরাট দামি গাড়ি হবে। কলকাতায় বড় বাড়ি হবে। বিদেশে বেড়াতে যাওয়া হবে। সুন্দরী মেয়েরা ঘিরে থাকবে। অনেক টাকার স্বপ্ন দেখতাম।
—সুতরাং ব্যাংকলুঠ করা যাক, ঠিক করে ফেললি?
—ওটাই দেখলাম বেস্ট উপায় স্যার। আমার টার্গেট ছিল তিন-চার মাসে এক কোটি টাকা। বাবা আর ভাইদের সঙ্গে শুধু মাছের ব্যবসা করলে কোনওদিনই আর বেশি বড়লোক হওয়া যেত না।
—পাঁচটা মিলিয়ে তো লাখ পঞ্চাশেক মতো হয়েছিল। টার্গেটের মাত্র অর্ধেক…
—আর একটা বড় কাজ করে থেমে যেতাম স্যার।
গোয়েন্দাদের নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি হল। আরও একটা?
—সেটা কোথায়?
—মেট্রোর টাকা স্যার।
—কোন মেট্রো?
—বউবাজার মোড়ের কাছে একটা স্টেশন আছে না? নামটা ভুলে যাচ্ছি…
—সেন্ট্রাল?
—হ্যাঁ স্যার, সেন্ট্রাল… ওই স্টেশনের কাছে মাটির তলায় মেট্রোর অনেক টাকা রাখা হয় বলে খবর পেয়েছিলাম। ওই কাজটায় একবারে তিরিশ-চল্লিশ তো হতই।
ফের একে অন্যের দিকে তাকান অফিসাররা। সত্যিই আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাশস্টোর আছে একটা সেন্ট্রাল স্টেশনের প্রায় লাগোয়াই। অনেক টাকা থাকে। পুলিশের বন্দুকধারী থাকে পাহারায়। মেট্রো কর্তৃপক্ষের নিজস্ব গার্ডও থাকে। ছ’নম্বর ডাকাতিটা ওখানে হতে যাচ্ছিল?
—তা করলি না কেন কাজটা?
—আপনারা তো খুব দৌড়ঝাঁপ করছিলেন স্যার… তাই কিছুদিন চুপচাপ থেকে মামলা ঠান্ডা হওয়ার পর করব ভেবেছিলাম। লেকটাউনের যে ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিয়েছিলাম আটমাস আগে, ওখানেই থাকতাম ম্যাক্সিমাম টাইম।
—বাড়ির লোক জানত, তুই ডাকাতি করে বেড়াচ্ছিস? বাবা? ভাই?
—বাবা পুরোটা জানত না। বড়দাও না। তবে আন্দাজ করত কিছু একটা গোলমালে জড়িয়ে পড়েছি। না হলে হুট করে বাজার-মসজিদ বানানোর এত টাকা পাব কোথায়? তবে সেজোভাই ওয়াহেদ জানত। ওর হাত দিয়ে লাখখানেক টাকা পাঠিয়েছিলাম একবার। বাড়িতে লুকিয়ে রাখতে।
—বাড়িতে কোথায়?
আকুঞ্জি চুপ করে থাকেন মিনিটখানেক। সামান্য দ্বিধাগ্রস্ত দেখায়। আমিনুলের হুমকিতে সংবিৎ ফেরে।
—শোন, বাড়িতে টাকা থাকুক আর না-ই থাকুক, তুই বলিস আর না-ই বলিস, আমরা আবার যাব ধামাখালিতে। তোকে সঙ্গে নিয়েই যাব। তোর সুস্থ হয়ে ওঠার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এবার পুরো তিনবিঘে জমি খুঁড়ে দেখব। প্রথমবার তো অত সময় হয়নি।
—ধানের পোয়ালের নীচে মাটিতে পুঁতে রাখতে বলেছিলাম ওয়াহেদকে।
‘পোয়াল’ বলতে ধানের স্তূপ। মাটি খুঁড়ে পাওয়াও গেল এক লক্ষ পঁচিশ হাজার, আকুঞ্জির বাড়িতে ফের রেইড করে।
পাঁচটা ঘটনায় মোট লুঠ হয়েছিল আটচল্লিশ লক্ষ আটশো পঁচিশ টাকা। যার মধ্যে উদ্ধার হয়েছিল কুড়ি লক্ষ দশ হাজার পাঁচ টাকা। যার সিংহভাগ কালিন্দীর ফ্ল্যাট থেকে। বাকি টাকার কিছুটা উদ্ধার হয়েছিল আন্দুলের কাছে একটা ফ্ল্যাট থেকে। যেটা ভাড়া নিয়েছিল আকুঞ্জি, যার সন্ধান জানত আবদুল।
টাকার বখরা? আকুঞ্জি বাকিদের বুঝিয়েছিল, তার কাছে লুঠের টাকা থাকাটাই নিরাপদ। তার কাছে অনেক জায়গা আছে লুকিয়ে রাখার। শেষ ডাকাতিটা হয়ে গেলে চূড়ান্ত ভাগবাটোয়ারা হবে। আবদুল এবং অন্যদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিল সাকুল্যে পঞ্চাশ হাজার। এবং নিজে নিয়ম করে টাকা ওড়াচ্ছিল মদ এবং মহিলার পিছনে।
পাঁচটা কেসেই চার্জশিট জমা পড়েছিল যথাসম্ভব দ্রুত। বহুসংখ্যক আঙুলের ছাপ সংগ্রহ করা হয়েছিল ডাকাতির জায়গাগুলো থেকে। যার কোনও না কোনওটা ম্যাচ করে গিয়েছিল ধৃত ছয় ডাকাতের ফিঙ্গারপ্রিন্টের সঙ্গে। বিচার চলাকালীন ঘটনাগুলোর সময় উপস্থিত একাধিক সাক্ষী সংশয়াতীত ভাবে ধৃতদের চিহ্নিত করেছিলেন Test Identification Parade-এ। আর বাজেয়াপ্ত টাকার বান্ডিলে ব্যাংকের স্লিপ তো ছিলই। আদালতে বিচারকের কাছে স্বীকারোক্তিও দিয়েছিল আবদুল হাই, সমস্ত কিছু কবুল করে। আকুঞ্জি পরিবারের সেজোছেলে ওয়াহেদের বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল অপরাধীর অপরাধমূলক কাজের কথা জেনেও তা গোপন করার অভিযোগ (harbouring a criminal)।
আকুঞ্জি এবং অন্য পাঁচ ডাকাতের দোষী সাব্যস্ত হওয়া স্রেফ সময়ের অপেক্ষা ছিল। যাবজ্জীবন কারাবাসের সাজা ঘোষিত হয়েছিল দু’বছরের মধ্যেই। ওয়াহেদের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল দশ বছরের কারাবাস।
কাহিনি এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু ‘পুনশ্চ’ এখনও বাকি। আকুঞ্জি পালানোর চেষ্টা করেছিল বিচার চলাকালীন। আলিপুর কোর্টে পুলিশের হাত ছাড়িয়ে মরিয়া দৌড় দিয়েছিল একদিন। একশো মিটার ধাওয়া করে ফিলমি কায়দায় ধরে ফেলেছিলেন এক শক্তসমর্থ কনস্টেবল।
সবে তিরিশ পেরনো আকুঞ্জি তীব্র অবসাদে ভুগতে শুরু করেছিল জেলে। কথা বলত না কারও সঙ্গে। খাওয়াদাওয়ার সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছিল বললেই চলে। পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল নীরোগ শরীরে। জেলযাপনে একের পর এক ব্যাধি বাসা বেঁধেছিল অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। আকুঞ্জি মারা গিয়েছিল সাজার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই।
প্রবাদের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না কখনও কখনও। লোভে পাপ। আর পাপে যা হওয়ার, তা- ই।
২.০৪ শরীর, শুধু শরীর?
[লীনা সেন হত্যা
বৈদ্যনাথ সাহা, উপনগরপাল, ষষ্ঠ সশস্ত্র বাহিনী। ২০১৩ সালে ভারত সরকারের ‘ইন্ডিয়ান পুলিশ মেডেল’-এ সম্মানিত।]
প্রদীপকুমার সেন। ভিজিটর্স স্লিপে নামটা দেখে সামান্য ভুরু কুঁচকে যায় নগরপালের। চেনেন দর্শনপ্রার্থীকে। সামাজিক জমায়েতে দেখা হয়েছে একাধিকবার। সখ্য নেই তেমন। হঠাৎ দেখায় ‘হাই-হ্যালো’ আছে। হতে পারে কোনও ব্যক্তিগত দরকারে এসেছেন বা কোনও অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ জানাতে। কিন্তু স্লিপে ‘Purpose of visit’-এর জায়গায় ‘Most urgent and confidential’ লেখা কেন? হঠাৎ লালবাজারে, সকাল দশটা বাজতে না বাজতেই? স্লিপটা হাতে রেখেই বেল বাজান পুলিশ কমিশনার।
—কল হিম ইন।
বিধ্বস্ত চেহারাটা যখন ঘরে ঢুকছে, একটু অবাকই হন নগরপাল। দেখলে বোঝা যায়, কাঁচাপাকা চুলের প্রৌঢ় ষাটের চৌকাঠ পেরিয়ে গেছেন। সুঠাম চেহারা হয়তো নয়, কিন্তু স্বাস্থ্যবান। লম্বায় নিশ্চিতভাবে ছ’ফুটের উপর। টাক পড়েছে সামান্য। চেহারায় একটা জেল্লা আছে। তবে আজ চলনেবলনে ছিটেফোঁটাও নেই চাকচিক্যের। যেন এক ধাক্কায় ভদ্রলোকের বয়স বেড়ে গেছে বছর দশেক। চোখ লাল। ঘুম সঙ্গ ত্যাগ করলে যেমন হয়, তেমন।
—কী ব্যাপার মি. সেন, হোয়াট ব্রিংস ইউ হিয়ার? অল ওয়েল?
নগরপালের প্রশ্নের উত্তরে বিন্দুমাত্র ভূমিকা করেন না প্রৌঢ়। সোজাসুজি পয়েন্টে আসেন, গলায় ঝরে পড়ে অসহায় আর্তি।
—স্যার, প্লিজ় হেল্প মি। মাই ওয়াইফ ইজ় মিসিং…
—মানে?
—ইয়েস স্যার, আমার স্ত্রীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না দু’দিন হল। বাড়ি থেকে পরশু বেরিয়েছিল। আর ফেরেনি।
—দাঁড়ান দাঁড়ান, ফেরেননি মানে? আপনারা থাকেন কোথায়? মিসিং ডায়েরি করেছেন?
—হ্যাঁ, যাদবপুর থানায়। আমরা প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শা রোডে থাকি। স্যার, লীনা মিসিং ফর দ্য লাস্ট টু ডেজ়… হাতে মুখ ঢেকে প্রায় কেঁদেই ফেলেন প্রৌঢ়। ফের বেল বাজানোর প্রয়োজন পড়ে নগরপালের। জল আনতে বলেন আরদালিকে।
—মি. সেন, যাদবপুর তো রাজ্য পুলিশের এলাকায়। আপনি চিন্তা করবেন না, আমি দেখছি। কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হল কিনা সেটা আগে খোঁজ নেওয়া দরকার। প্লিজ় স্যার, থানা বলছে, মিসিং ডায়েরির এনকোয়ারি চলছে। আমি এখন কী করব, মাথা কাজ করছে না।
—মোবাইল নম্বরটা… মানে আপনার মিসেসের?
—ছিল না। আমরা কেউই মোবাইল ব্যবহার করি না।
চিন্তিত দেখায় নগরপালকে। লালবাজার পিবিএক্স-কে ধরেন ইন্টারকমে।
—ডিসি ডিডি প্লিজ়…
.
কড়েয়া থানার গাড়ি যখন ব্রেক কষল অভিজাত বহুতলের সামনে, ফুটপাথে ছোটখাটো জটলা কৌতূহলী জনতার। নেমে চারপাশে একঝলক তাকান ওসি। জটলাকে ভিড়ে পরিণত হতে দিলে সে ভিড় খুব তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে আসবে। ট্র্যাফিকের ঘোর সমস্যা হবে। এমনিতেই ঘড়িতে বিকেল পাঁচটা। অফিসফেরত গাড়ির ঢল নামল বলে। ওয়ারলেসে থানায় নির্দেশ পাঠান বড়বাবু, বাড়তি ফোর্স দরকার এখানে। ক্রাউডকে সরিয়ে দিতে বলুন। কুইকলি!
‘মৈনাক অ্যাপার্টমেন্টস’। পি-১৭ বি, আশুতোষ চৌধুরী অ্যাভিনিউ। বালিগঞ্জ ফাঁড়ি থেকে পার্ক সার্কাসের দিকে কিছুটা হাঁটলেই ডানদিকে চোখে পড়তে বাধ্য এগারো তলার বাড়িটা। ঢোকার মুখেই বড় গেট। এ ধরনের আবাসনে যেমন থাকে। ঢুকেই ছোট একটা ড্রাইভওয়ে। যার শেষে কুড়ি-পঁচিশটা গাড়ি রাখার মতো পার্কিং স্পেস।
‘সিকিউরিটি এনক্লোজার’ রয়েছে একটা। কেয়ারটেকারের বসার ব্যবস্থা সেখানেই। কাচ দিয়ে ঘেরা। ভিতর থেকে স্বচ্ছন্দে দেখা যায় বাইরেটা। কে ঢুকছে, কে বেরচ্ছে, সব। দুটো সিঁড়ি। একটা ব্যবহার হয়ই না প্রায়। তালা বন্ধ থাকে। ওই সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে আবাসিকদের বাড়ির কাজের লোকদের ঘর। মূল সিঁড়ির পাশেই দুটো লিফট। লিফটম্যান আছে, তবে চাইলে নিজেরাও অপারেট করতে পারেন আবাসিকরা। ওসি-কে দেখতে পেয়েই শশব্যস্ত লিফটম্যান এগিয়ে আসে, গলায় উত্তেজনার আঁচ, ‘আসুন স্যার, দশতলায়।’
ফ্ল্যাট নম্বর ৯০৬। যার বাইরে অন্তত পনেরো-কুড়ি জনের জটলা-গুঞ্জন-ফিসফাস। লিফট থেকে বেরিয়েই পকেটে হাত চলে যায় ওসি-র। রুমাল বের করতে বাধ্য হন। প্রবল দুর্গন্ধ গ্রাস করেছে চারদিক। এবং গন্ধের উৎসমুখ যে ওই ফ্ল্যাটই, সন্দেহের বিশেষ অবকাশ নেই। ওই গন্ধ পেয়েই ফোন গিয়েছিল থানায়।
গোদরেজের ইয়া বড় তালা ঝুলছে ফ্ল্যাটের দরজায়। ওসি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সামনে উপস্থিত কেয়ারটেকার জানিয়ে দিলেন, ডুপ্লিকেট চাবি নেই। চাবি থাকত ‘দিদিমণির’ কাছেই। তালা ভেঙে ঢোকার পর আবিষ্কৃত হল দিদিমণি-র মৃতদেহ। বহু ডেডবডি দেখার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বড়বাবুও মুহূর্তের জন্য হতবাক হয়ে পড়লেন দৃশ্যের বীভৎসতায়।
আঁতকে না ওঠাই আশ্চর্য, গা গুলিয়ে না ওঠাই অস্বাভাবিক। দশ আর এগারো তলা মিলিয়ে ডুপ্লে ফ্ল্যাট। একটা দরজা দশ থেকে এগারোয় যাওয়ার। তালা বন্ধ। দশতলার ফ্ল্যাটটা বেশি বড় নয়, কিন্তু ছিমছাম। বাহুল্য না থাক, পারিপাট্য আছে। একটা শোওয়ার ঘর, ছোট। বসার ঘরে কার্পেট-সেন্টার টেবিল-সোফাসেট, যেমন থাকার। বারান্দা রয়েছে একফালি। রয়েছে বসার ঘরের লাগোয়া বাথরুম এবং রান্নাঘর। অসহনীয় দুর্গন্ধের উৎপত্তি যে ওই রান্নাঘর থেকেই, আবিষ্কৃত হল নিমেষেই। রান্নাঘরের দরজা বাইরে থেকে ভেজানো। ঠেলে খুললেন ওসি, এবং পিছনে দাঁড়ানো এক প্রতিবেশী আবাসিকের মুখ থেকে ছিটকে বেরল আতঙ্কিত আর্তনাদ, ও মাই গড!
এক মহিলা নিস্পন্দ বসে আছেন পা ছড়িয়ে। সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা। দেখে মনে হয়, বয়স চল্লিশের কোঠায়। মাথাটা দেওয়ালে ঠেস দেওয়া। হাত দুটো বাঁধা নারকেল দড়ি দিয়ে। মুখে একটা কাপড় গোঁজা। তীব্র পচন ধরেছে দেহে। পোকার থিকথিক-ভনভন সর্বাঙ্গে। চোখ ঠেলে বেরিয়ে এসেছে কোটর থেকে। দেহ ফুলে গিয়ে সে এক বীভৎস আকার নিয়েছে। শরীর থেকে বেরিয়ে এসেছে বর্জ্য তরল। রক্তের ধারা জমাট বেঁধেছে মেঝে জুড়ে। দমবন্ধ হয়ে আসার জোগাড়, এতই দাপট দুর্গন্ধের।
প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসা করেন বড়বাবু, কে ইনি? ইনিই থাকতেন এ ফ্ল্যাটে? ঝটিতি উত্তর দেন কেয়ারটেকার, ‘দিদিমণি। লীনা দিদিমণি।’
.
লীনা সেন হত্যা মামলা। কড়েয়া থানা, কেস নম্বর ১৩৬/ তারিখ ০৩.০৭.১৯৯৯। ধারা, ৩০২/২০১ আইপিসি। খুন এবং প্রমাণ লোপাট। বালিগঞ্জের অভিজাত বহুতলে মধ্যবয়সি মহিলার নৃশংস হত্যা এবং পচন-ধরা বিবস্ত্র দেহ উদ্ধার। চাঞ্চল্য উৎপন্ন হওয়ারই কথা। হয়েওছিল। ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মিডিয়া, শহরে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল ‘মৈনাক অ্যাপার্টমেন্ট’।
হুলুস্থুল ফেলে দেওয়া খুন। তদন্তের ভার ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের হাতে তুলে দিতে সময় নিলেন না নগরপাল। রহস্যভেদের দায়িত্ব পড়ল গোয়েন্দাবিভাগের তৎকালীন সাব-ইনস্পেকটর (বর্তমানে ষষ্ঠ সশস্ত্র ব্যাটালিয়নের ডেপুটি কমিশনার) বৈদ্যনাথ সাহার উপর।
দ্রুত খবর পাঠানো হল FSL (ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি)-এ। তলব করা হল ডগ স্কোয়াডকে। পুলিশ ট্রেনিং স্কুল থেকে ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দিল পুলিশ কুকুর। ডিসি ডিডি স্বয়ং খবর পেয়েই ছুটলেন হোমিসাইড বিভাগের অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে। তাঁর আগেই পৌঁছে গিয়েছেন ডিসি সাউথ। শুরু হয়ে গিয়েছে প্রাথমিক তথ্যতালাশ। মৃতার দেহ যখন নীচে নামিয়ে এনে পুলিশ ভ্যানে তোলা হচ্ছে ময়নাতদন্তে পাঠানোর জন্য, রাস্তায় ভিড় জমে গিয়েছে অন্তত শ’দুইয়ের। কড়েয়া থানার ফোর্স হিমশিম খাচ্ছে সামলাতে। বাড়তি ফোর্স রওনা দিয়েছে লালবাজার থেকে।
ঘটনার ঘনঘটায় ঢোকার আগে জরুরি তথ্য কিছু। এক, এগারো তলাতেও যাওয়া হল তালা ভেঙে। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা দুটো তলাই তন্নতন্ন করে পরীক্ষা করে জানিয়ে দিলেন, ‘no external interference into the flat’। বাইরে থেকে ঢুকে কোনরকম জোরজবরদস্তির চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। সংগ্রহযোগ্য এক বা একাধিক হাত বা পায়ের ছাপ পাওয়া যাচ্ছে না ঘরের আসবাবপত্র-বাসনকোসনে। একটা আলমারি ছিল ঘরে। সেটাও অক্ষত, ভাঙার কোনও চেষ্টা হয়নি। খুব মূল্যবান কিছু ছিল না ঘরে আপাতদৃষ্টিতে। আর থাকলেও তা যে আততায়ী বা আততায়ীদের অভীষ্ট ছিল না, স্পষ্ট। ডাকাতি জাতীয় কিছু হওয়ার সম্ভাবনা কম। কার্পেটে খয়েরি তরলের যে ছোপ দেখা যাচ্ছে দু’-এক জায়গায়, ওটা শুকিয়ে যাওয়া রক্তের দাগ। তবে ‘স্যাম্পল’ সংগ্রহ করলেও ওটা যে রক্তই, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় একশো শতাংশ নিশ্চিতভাবে বলা মুশকিল হবে। পুলিশ কুকুর এল, দেখল এবং ফিরে গেল। ঘ্রাণযোগ্য তেমন কিছু সূত্র অমিল।
দুই, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ফরেনসিক বিভাগের প্রধান অজয়কুমার গুপ্তের তত্ত্বাবধানে হওয়া ময়নাতদন্তের রিপোর্ট জানাল, শ্বাসরোধ হয়েই মৃত্যু। মুখ এবং নাক চেপে ধরার চেষ্টা হয়েছিল বলপূর্বক। ড. গুপ্ত লিখলেন, ‘The death in my opinion was due to the effect of asphyxia as a result of gagging ante-mortem and homicidal in nature, there was also attempt of closing mouth and nostrils forcibly.’ যেমনটা ভাবা হয়েছিল।
খুনের আগে যৌন অত্যাচার? হয়নি। স্পষ্ট হয়ে গেল সংগৃহীত ‘vaginal swab’-এর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায়। খুনটা হয়েছিল কখন? বিশেষজ্ঞরা জানালেন, ২৯ জুন দুপুর থেকে সন্ধের মধ্যে। মনে করিয়ে দিই মামলা রুজু হওয়ার তারিখটা, ৩ জুলাই। যেদিন সন্ধে ছুঁইছুঁই বিকেলে লীনার মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়েছিল।
তিন, P.O. (Place of Occurrence) থেকে বাজেয়াপ্ত হওয়া জিনিসের মধ্যে থাকল মৃতার হাত বাঁধার জন্য ব্যবহৃত নারকেল দড়ি, মুখে গোঁজা কাপড়, রান্নাঘরের মেঝে এবং কার্পেটে জমাট বাঁধা খয়েরি দাগের নমুনা, যে তালা ভেঙে ফ্ল্যাটে ঢোকা হয়েছিল, সেটা, আরও কিছু টুকিটাকি। এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, একটি ছোট ডায়েরি। লীনা সেনের।
ডায়েরির বিষয়বস্তুতে পরে আসছি। তার আগে প্রাথমিক পরিচয় করিয়ে দেওয়া দরকার মামলার কেন্দ্রে থাকা চরিত্রদের সঙ্গে।
লীনা সেনের জন্ম পাঁচের দশকের গোড়ায়। খুন হওয়ার সময় বয়স হয়েছিল সাতচল্লিশ। জন্ম লীনা মুখার্জি হিসাবে। সাত বছরের ছোট ভাই বর্তমান। নাম অমিত। লীনা কিশোরীবেলা থেকেই ছিলেন বহির্মুখী প্রকৃতির। অত্যন্ত সপ্রতিভ, সুন্দরী। কনভেন্ট-শিক্ষিতা, অনার্স গ্র্যাজুয়েট। প্রেম করে বিয়ে করলেন দক্ষিণ ভারতীয় যুবক বব শেষাদ্রিকে, বয়স যখন চব্বিশ। বিয়ের বছর দুয়েক আগে থেকেই লীনা চাকরি করতে শুরু করেছিলেন নামকরা বেসরকারি বাণিজ্যিক সংস্থায়। কর্মস্থল বদলেছিলেন ঘনঘন। কোথাও স্টেনোগ্রাফার, কোথাও রিসেপশনিস্ট, কোথাও বা জনসংযোগ আধিকারিক। মৈনাক অ্যাপার্টমেন্ট-এর ডুপ্লে ফ্ল্যাটটি ভাড়া নিয়েছিলেন বিয়ের কয়েক মাস আগে। বিয়ের পর ওই ফ্ল্যাটেই দাম্পত্য জীবন শুরু হয়েছিল বব-লীনার।
বিবাহজীবন সুখের হয়নি। এক বছরের মধ্যেই ডিভোর্স। দ্বিতীয় বিয়ে প্রায় কুড়ি বছর পরে। ’৯৫-এর অগস্টে। যাঁর সঙ্গে দ্বিতীয় বিয়ে, তিনিও বিবাহবিচ্ছিন্ন। প্রদীপকুমার সেন, পেশায় চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট। নামকরা বাণিজ্যিক সংস্থার ডাকসাইটে বড়কর্তা। লীনা ছিলেন প্রদীপের পারসোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। কর্মসূত্রেই গাঢ় হয় ঘনিষ্ঠতা, পরিণতি বিয়েতে। প্রদীপবাবুর ফ্ল্যাট ছিল যাদবপুর থানা এলাকার প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শা রোডে, ‘নয়নতারা অ্যাপার্টমেন্ট’-এ। বিয়ের পর সেখানে গিয়ে উঠলেও লীনা ছাড়েননি বালিগঞ্জের ভাড়া নেওয়া ফ্ল্যাটটা।
দেহ আবিষ্কৃত হওয়ার পর খবর দেওয়া হল প্রদীপবাবুকে। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর ক্যামাক স্ট্রিটে নিজের ফার্ম খুলেছেন। ছুটে এলেন অফিস থেকে এবং মৃতা লীনাকে দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। ফ্ল্যাট থেকে যখন সবাইকে বার করে দেওয়া হচ্ছে ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য, তখনও সোফা ছেড়ে উঠতে পারছেন না বাক্রুদ্ধ প্রদীপ। দুই পুলিশকর্মী ধরে ধরে নিয়ে গেলেন লিফট পর্যন্ত। ডিসি ডিডি ভদ্রলোককে দেখেই চিনলেন। ইনিই তিনি, যাঁকে পুলিশ কমিশনারের ঘরে দেখেছিলেন দিন দুয়েক আগে। যিনি পয়লা জুলাই লালবাজারে নগরপালের কাছে জানিয়েছিলেন আর্জি, ‘আমার স্ত্রী-কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, হেল্প মি প্লিজ়।’
বৈদ্যনাথ শুরু করলেন তথ্যসংগ্রহের কাজ। দিব্যি বুঝতে পারছিলেন, দ্রুত কিনারা করার চাপ এই মামলায় অবশ্যম্ভাবী। প্রাথমিক জেরায় যে যতটা বললেন, ফিরে দেখা যাক। যতটা বললেন, তার বাইরেও যা যা জানা যাচ্ছিল পুলিশি তদন্তে, সেটাও থাকুক। সামগ্রিক ছবিটা স্পষ্ট হবে।
প্রদীপকুমার সেনের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর যেভাবে এগোল, সারাংশ তুলে দিচ্ছি।
—মি. সেন, যদি কিছু না মনে করেন, এটা তো দ্বিতীয় বিয়ে ছিল। প্রথমটা ভেঙে গেল কেন?
—মনে করার কী আছে? ফার্স্ট ওয়াইফ ছিল সুনন্দা। আমাদের এক ছেলে, এক মেয়ে। দু’জনেই বাইরে চাকরি করে। সুনন্দার সঙ্গে ডিভোর্স হয়েছে বছরচারেক আগে। বনিবনা হচ্ছিল না আমাদের। মিউচুয়াল কনসেন্টে ডিভোর্স।
—লীনা তো আপনার পিএ ছিলেন বিয়ের আগে, না?
—হ্যাঁ। বিয়ের পর চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল। আমিই জোর করেছিলাম। ভাড়াবাড়িটাও ছেড়ে দিতে বলেছিলাম। রাজি হয়নি।
—সম্পর্ক কেমন ছিল আপনাদের?
—টাকাপয়সা নিয়ে মাঝে মাঝে অশান্তি হত। লীনা হাইপ্রোফাইল লাইফ পছন্দ করত। আমি মাসে মাসে হাতখরচের জন্য যথেষ্ট টাকা দিতাম। কিন্তু লীনার তাতে কুলোত না। এই নিয়ে মাঝে মাঝে ঝগড়া হত কখনও কখনও। মিটেও যেত। উই ওয়্যার ইন লাভ উইথ ইচ আদার। ইন ফ্যাক্ট, গত মাসের শুরুর দিকে সপ্তাহখানেকের জন্য সিঙ্গাপুর বেড়াতে গিয়েছিলাম আমরা। দারুণ কেটেছিল ছুটিটা।
—কাউকে সন্দেহ হয়? কে মারতে পারে মিসেস সেনকে?
—নো ক্লু। অ্যাবসোলিউটলি নো ক্লু। আমি জাস্ট ভাবতেই পারছি না…
—২৯ জুন, মানে মার্ডারের দিন, স্ত্রী-র সঙ্গে শেষ কখন দেখা হয়েছিল? আর ওইদিন আপনার মুভমেন্টটা একটু ডিটেলে জানা দরকার।
—সার্টেনলি। সেদিন আমাদের একসঙ্গে লাঞ্চ করার কথা ছিল তাজ বেঙ্গলে। আড়াইটে নাগাদ টেবিল বুক করেছিলাম।
—হুঁ…
—আমি রোজকার মতো সাড়ে ন’টা নাগাদ অফিস বেরলাম। কথা ছিল, লীনা ট্যাক্সি নিয়ে অফিসে চলে আসবে দেড়টা নাগাদ। সেখান থেকে তাজে যাব। লীনা যখন পৌনে দুটো পর্যন্ত এল না, বাড়িতে ফোন করলাম। কাজের লোক বলল, মেমসায়েব দশটার একটু পরে বেরিয়ে গেছেন।
—তারপর?
—হপ্তায় দু’-একদিন লীনা মৈনাক-এ যেত ইদানীং। ফ্ল্যাটের রিনোভেশন হচ্ছিল। মিস্ত্রিদের যাওয়া-আসা ছিল। নতুন করে সাজাচ্ছিল ফ্ল্যাটটা। আমি ভাবলাম ওখানেই গেছে হয়তো। আসতে দেরি হচ্ছে কোনও কারণে।
—আচ্ছা…
—গাড়ি নিয়ে নিজেই মৈনাক-এ গেলাম। এই দুটো-সোয়া দুটো হবে তখন। খুব বৃষ্টি হচ্ছিল সেদিন। লীনা ফ্ল্যাটেই ছিল। বলল, রিপেয়ার ওয়ার্ক সব ঠিকঠাক হয়েছে কিনা, আরও কিছু খুঁটিনাটি কাজ আছে কিনা, দেখতে এসেছিল। বৃষ্টি হচ্ছিল বলে বেরতে পারেনি।
—সেদিনই শেষ দেখা ওঁর সঙ্গে?
—হ্যাঁ। এত বৃষ্টি হচ্ছিল যে বলার নয়! আমরা লাঞ্চ ক্যানসেল করলাম। লীনা থেকে গেল ঘরটা গোছগাছ করবে বলে। আমার অফিসে কাজ ছিল। ফিরে এলাম আধঘণ্টা পর। সেই শেষ দেখা ওর সঙ্গে।
—লীনা আর বাড়ি ফেরেননি?
—না। বলেছি তো আগে। আমার বাড়ি ফিরতে প্রায় রাত দশটা হয়েছিল। এসে দেখলাম, লীনা ফেরেনি। সারা রাত ফিরল না।
—পুলিশে জানালেন না? মৈনাক-এ গেলেন না কেন রাতেই?
—পুলিশে তো পরদিন দুপুরেই জানালাম। যাদবপুর থানায় মিসিং ডায়েরি করলাম। তেমন গুরুত্ব দিল না থানা। অফিসার বললেন, এনকোয়ারি হবে। একটা ফোটো শুধু নিয়ে রাখলেন।
—বুঝলাম, কিন্তু সে-রাতেই তো মৈনাক-এ যেতে পারতেন?
—ভাবলাম, রাতটা দেখি। লীনার মা থাকেন সুন্দরীমোহন অ্যাভিনিউতে। ভাবলাম, হয়তো ওঁর শরীর হঠাৎ খারাপ হয়েছে। খবর পেয়ে গেছে ওখানে। হয়তো শাশুড়ি জোর করেছেন থেকে যেতে রাতটা। শাশুড়ির শরীরটা ইদানীং ভাল যাচ্ছিল না। প্রতি সপ্তাহেই এক-দু’বার যেত লীনা ওবাড়িতে। ভাবলাম…
—আপনার শাশুড়ির বাড়িতে ফোন নেই? এত কিছু ভেবে না নিয়ে ফোন তো করতে পারতেন একটা।
—করেছিলাম। কানেক্ট করতে পারিনি। জল জমলে শহরের ফোনের কী দশা হয় সে তো জানেনই। আমার অফিসের ফোনও সেদিন দুপুর থেকে ডেড।
—বেশ, তারপর?
—সেই রাতে একফোঁটা ঘুমোতে পারিনি দুশ্চিন্তায়। পরদিন সকালে, এই দশটা নাগাদ আবার গেলাম মৈনাক-এ। দেখলাম, তালা বন্ধ। লীনার কাছেই একমাত্র চাবি থাকত ফ্ল্যাটের। অফিস ফিরে ড্রাইভারকে পাঠালাম সুন্দরীমোহন অ্যাভিনিউয়ে লীনার মায়ের বাড়ি। ওখানেও নেই। আসেইনি। সোজা যাদবপুর থানায় গিয়ে ডায়েরি করলাম। সেদিনও ফিরল না লীনা। পরদিন মাথা কাজ করছিল না আমার। আর কোনও উপায় না দেখে সকাল-সকাল সোজা সিপি সাহেবের কাছেই ছুটলাম। তারপর তো সবটাই জানেন…
দৃশ্যতই ক্লান্ত দেখায় প্রদীপকে। আরও জিজ্ঞাসাবাদ করা দরকার ভদ্রলোককে, ভাবেন বৈদ্যনাথ। আরও তথ্য আসুক হাতে, তারপর দেখা যাবে।
তথ্য এলও পরের কয়েকদিন দৌড়ঝাঁপের পর। যা প্রদীপ বলেননি প্রাথমিক জেরার সময়। প্রথম, লীনার মা জানালেন, মেয়ের সঙ্গে জামাইয়ের সম্পর্ক গত কয়েক মাসে তলানিতে এসে ঠেকেছিল। চাকরি যখন ছেড়েছিলেন, লীনা মাইনে পেতেন মাসিক পনেরো হাজার। আজ থেকে প্রায় বাইশ-তেইশ বছর আগে মাসে হাজার পনেরো মানে অনেক। বিলাসবৈভবের পক্ষে যথেষ্ট। বিয়ের পর চাকরি ছাড়তে বাধ্য হওয়ায় স্বামীর উপর আর্থিকভাবে নির্ভর হয়ে পড়েছিলেন সম্পূর্ণ। প্রদীপ মাস গেলে তিন হাজার দিতেন লীনাকে। সেই নিয়েই সূত্রপাত অশান্তির। দুর্ব্যবহার তো ছিলই। গায়েও হাত তুলতেন মাঝেমাঝেই, মায়ের কাছে অনুযোগ করতেন লীনা।
দ্বিতীয়, নিজের কিছু গয়নাগাটি মেয়ের কাছে রেখেছিলেন লীনার মা। বিয়ের পর সেগুলো ফেরত দিতে চাননি প্রদীপ। লীনা এবং তাঁর মায়ের শত অনুরোধেও। এ নিয়েও অশান্তি হত প্রায়ই।
তৃতীয়, লীনার চরিত্রের দিকে নিয়মিত আঙুল তুলতেন প্রদীপ। যিনি সম্প্রতি ক্যালকাটা ক্লাবের প্রেসিডেন্ট পদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এবং গো-হারান হেরেছিলেন। লীনার সঙ্গে সামাজিক স্ট্যাটাসের এতটাই তফাত তাঁর, এবং লীনার বেহিসাবি জীবনযাপন এতটাই প্রচারিত, সেজন্যই ভোট পাননি সংখ্যাগরিষ্ঠের, এমনই বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল প্রদীপের।
লীনার যে ডায়েরি পুলিশ পেয়েছিল ফ্ল্যাট থেকে, তাতেও ধরা ছিল অসুখী দাম্পত্যের রোজনামচা। কখনও ইংরেজিতে লিখতেন, কখনও কখনও বাংলায়। লেখার সিংহভাগ জুড়ে প্রদীপের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, চাকরি ছেড়ে দেওয়ার আক্ষেপ এবং টাকাপয়সার টানাটানির বৃত্তান্ত। ভাড়া বাড়ানোর জন্য বাড়িওয়ালার তাগিদ ক্রমে অসহনীয় হয়ে ওঠার উল্লেখও রয়েছে ডায়েরির পাতায়।
বাড়িওয়ালার পরিচয় প্রয়োজন এখানে। ডাক্তার স্বয়ম্ভু মুখার্জি। থাকেন মৈনাক থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে, ওল্ড বালিগঞ্জ রোডে। ফ্ল্যাট থেকে দুর্গন্ধ বেরচ্ছে দেখে আবাসিকরা ৩ জুলাই বিকেলে ডা. মুখার্জিকে ফোন করেছিলেন। তিনিই ফোনে যোগাযোগ করেন কড়েয়া থানার সঙ্গে।
ডা. মুখার্জি জানালেন, হ্যাঁ, অনেকদিন বাড়ির ভাড়া বাড়াননি লীনা। বারবার বললেও কর্ণপাত করতেন না। কয়েক বছর আগে উচ্ছেদের মামলাও করেছিলেন। কিন্তু বাড়িওয়ালা-ভাড়াটের মামলা যেমন চলতে থাকে অনন্তকাল, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। ভাড়া নিয়ে লীনার সঙ্গে কয়েক বছর আগে বাদানুবাদ হয়েছিল, কিন্তু ওই পর্যন্তই।
শুধু ‘ওই পর্যন্তই’ যে নয়, শীঘ্রই জানতে পারলেন বৈদ্যনাথ। স্রেফ বাদানুবাদ নয়, বাড়িওয়ালা-ভাড়াটের সম্পর্ক চূড়ান্ত তিক্ততায় পৌঁছেছিল বছর সাতেক আগে। মৈনাক-এর আবাসিকদের মিটিংয়ে স্বয়ম্ভু চোটপাট করেছিলেন লীনার বেপরোয়া জীবনযাপন নিয়ে। ফ্ল্যাটে যখন-তখন একাধিক পুরুষের যাতায়াত নিয়ে গলা চড়িয়েছিলেন, ‘আমার ফ্ল্যাটে এসব নোংরামো চলবে না!’ তুমুল তর্কাতর্কি হয়েছিল। লীনা পালটা বলেছিলেন, ‘আমার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আপনি বলার কে? ফ্ল্যাটের ভাড়ার টাকা গুনে দিচ্ছি, ব্যস! আমার জীবন আমি যেমন খুশি কাটাব। আপনি কে নাক গলানোর?’
এই অশান্তির কিছুদিন পরই লীনার বাড়িতে পুলিশ এসেছিল এক রাতে। ফ্ল্যাটে মধুচক্র চলছে, এই অভিযোগের তদন্তে। লীনাকে নিয়েও যাওয়া হয়েছিল থানায়, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। কাগজেও বেরিয়েছিল ঘটনার খবর। লীনার দৃঢ় ধারণা ছিল, পুলিশে অভিযোগটা স্বয়ম্ভুরই মস্তিষ্কপ্রসূত। এ নিয়েও ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল বিস্তর।
উচ্ছেদের মামলার কাগজপত্র ঘেঁটে বৈদ্যনাথ দেখলেন, লীনা যে দুশ্চরিত্রা এবং বাড়িতে দেহব্যবসা চালাচ্ছেন, সোজাসাপটা এমন অভিযোগ করেছিলেন স্বয়ম্ভু। পিটিশনের সঙ্গে ছিল ফ্ল্যাটে পুলিশি অভিযানের খবরের পেপারকাটিং।
স্বয়ম্ভু প্রথমে এসব কিছুই বলেননি। বরং জানিয়েছিলেন, উৎসাহ হারিয়েছিলেন মামলা নিয়ে। খবরই রাখেন না আর। জানতে চেয়েছিলেন বৈদ্যনাথ, ‘ঝামেলা যে কথা-কাটাকাটির থেকে অনেকটা বেশিই গড়িয়েছিল, বলেননি কেন আগে?’ সামান্য অসহিষ্ণু উত্তর এসেছিল, ‘অনেকদিন আগের কথা, মনেও ছিল না। আর এসব এই কেসে প্রাসঙ্গিক কি? বাড়িওয়ালা-ভাড়াটেতে এসব ঝামেলা তো হয়েই থাকে। আপনি কি বাই এনি চান্স আমাকে সন্দেহ করছেন? খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন, ২৯ তারিখ সারাদিন বাড়িতেই ছিলাম।’
খোঁজ নেওয়ার বাকি ছিল অনেক। দিনের মধ্যে নিয়ম করে চার-পাঁচ ঘণ্টা মৈনাক-এ কাটাচ্ছিলেন বৈদ্যনাথ। কাজ কি একটা? আবাসনে মোট চুয়ান্নটা ফ্ল্যাট। প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের নাম-ঠিকানা-পেশা ইত্যাদির তালিকা তৈরি করা। খুনের দিন কে কোথায় ছিলেন, কী করছিলেন, তার ‘ইনফর্মেশন শিট’ বানানো ঘণ্টার পর ঘণ্টার প্রশ্নোত্তরে। লীনার ফ্ল্যাটের মেরামতিতে যে মিস্ত্রিরা আসত-যেত, তাদের খোঁজ করে জেরা। এবং অপরাধের কোনও পূর্ব-ইতিহাস কারও আছে কিনা, যাচাই করে নেওয়া। ক্লাব-পার্টি-নাচাগানা-হইহই ছিল লীনার স্বভাবজাত। বন্ধুবৃত্তে কে কে ছিলেন তাঁর, কে কতটা ঘনিষ্ঠ ছিলেন তাঁদের মধ্যে, সে ব্যাপারে খবর জোগাড় করা বিনিদ্র দৌড়ঝাঁপে।
তদন্তের সনাতনী ব্যাকরণ মেনেই এগোচ্ছিলেন বৈদ্যনাথ। যে ব্যাকরণ বলে, তথ্যই শক্তি। কোনও তথ্যই তুচ্ছ নয়, এই ভেবে এগোও। যথাসাধ্য তথ্য মজুত করো। এবং তারপর কোন কোনটা জরুরি বা প্রাসঙ্গিক নয় একেবারেই, সেগুলো চিহ্নিত করো। সরিয়ে ফেলো চিন্তাস্রোত থেকে। ছবিটা আপনিই পরিষ্কার হয়ে আসবে। ছোট হয়ে আসবে তদন্তের বৃত্তটা, ভাবনা হবে স্বচ্ছতর।
বৃত্ত ছোট হওয়া দূরে থাক, রহস্য জটিলতর হল আবাসনের কর্মীদের জেরাপর্বে। মৈনাক-এর নিরাপত্তাব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ শুরুতে দিয়েছি। দুটো জিনিস যোগ করার। এক, আবাসনে কোনও সিসি টিভি ছিল না। ঢোকা-বেরনোর কোন প্রযুক্তি-প্রমাণ পাওয়ার প্রশ্ন নেই। দুই, যাঁরা আবাসনের বাসিন্দা, তাঁদের ‘ভিজিটর্স রেজিস্টার’-এ নাম না লেখালেও চলত। কিন্তু বহিরাগত হলে কোন ফ্ল্যাটে কার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন, রেজিস্টারে লেখা বাধ্যতামূলক। আবাসিকের সঙ্গে কোনও বহিরাগত এলে? নিয়মনাস্তি।
কেয়ারটেকার এবং অন্য নিরাপত্তাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলে বৈদ্যনাথ বুঝলেন, ব্যবস্থা নিশ্ছিদ্র তো নয়ই। বরং ঢিলেঢালা, দায়সারা। ব্যাট-প্যাডের মধ্যে দিয়ে বল গলে যাওয়ার মতো ফাঁক যথেষ্ট।
কেয়ারটেকারের নাম দিলীপ চ্যাটার্জি। একজন সহকারী আছেন, জয়প্রকাশ শর্মা। লিফটম্যান একজনই। নাম, বরুণ রায়। দিলীপ-জয়প্রকাশকে সাহায্য করার জন্য রয়েছেন একজন কর্মী, শংকর পণ্ডিত। নিরাপত্তারক্ষী মাত্র তিনজন। ভানু ব্যানার্জি, শম্ভু বড়ুয়া এবং অসিত পণ্ডিত। তিন শিফটে আট ঘণ্টা করে ডিউটি। সকাল ছ’টা থেকে দুপুর দুটো। দুটো থেকে রাত দশটা। দশটা থেকে সকাল ছ’টা পর্যন্ত নাইট শিফট। একজন লিফটম্যানের পক্ষে চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি করা অসম্ভব। বরুণ মৈনাক-এ থাকেন দুপুর দুটো থেকে রাত দশটা পর্যন্ত। বাকি সময় পালা করে লিফটম্যানের ভূমিকায় থাকেন জয়প্রকাশ-শংকর।
মোদ্দা কথা, লোক যেহেতু কম, পরিস্থিতি অনুযায়ী সবার কাজটাই সবাই কমবেশি করে থাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে। ২৯ এবং ৩০ তারিখ যাঁরা ডিউটিতে ছিলেন, সবার সঙ্গে কথা বলা হল বিস্তারিত। বাড়তি তথ্য বলতে, ২৯ তারিখ যখন এসেছিলেন মি. সেনের হাতে একটা মাঝারি সাইজের ফোলিও ব্যাগ ছিল। বেরনোর সময়ও ব্যাগটা সঙ্গে ছিল। আবাসিকদের ছাড়া অন্য কারও গাড়ি ভিতরে পার্ক করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ছিল মৈনাক-এ। ২৯ তারিখ প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল বলে প্রদীপ কেয়ারটেকার অফিসে এসে অনুরোধ করেন গাড়ি ভিতরে রাখতে দেওয়ার জন্য। ড্রাইভার ইসমাইল ভিতরেই পার্ক করেছিল প্রদীপের ছাইরঙা মারুতি এস্টিম।
লিফটে বরুণ দশতলায় পৌঁছে দিয়েছিলেন প্রদীপকে। নামিয়েও এনেছিলেন আধঘণ্টা পর। পরের দিন, ৩০ তারিখ সকালে প্রদীপ যখন এসেছিলেন, লিফটের দায়িত্বে ছিলেন শংকর। বরুণ-শংকর দু’জনের বিবরণের সঙ্গে প্রদীপের বয়ান মিলে গেল হুবহু। সেনসাহেবের আচরণে কোনও অস্বাভাবিকতা চোখে পড়েছিল? ‘না তো!’ দু’জনেই বললেন একবাক্যে। লীনা ২৯ তারিখ সেই যে সকাল দশটায় এসেছিলেন, তারপর দুপুর-বিকেলের মধ্যে আর বেরিয়েছিলেন? সেই একবাক্যেই উত্তর, ‘না, দিদিমণি তো আর বেরননি। বেরলে তো দেখতেই পেতাম।’
কী দেখতে পেতেন ওঁরা আর কী না পেতেন, সে অবশ্য বৈদ্যনাথ বুঝে গিয়েছিলেন খুনের দিনদুয়েকের মধ্যেই। মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল ৩ তারিখ। সাদা পোশাকে বৈদ্যনাথ ৫ তারিখ রাতে কাউকে কিছু না বলে একাই ঢুঁ মেরেছিলেন মৈনাক-এ। দেখেছিলেন, কেয়ারটেকার অফিসের সামনে নাইট শিফটের নিরাপত্তারক্ষী খুব মন দিয়ে চেয়ারে বসে ঢুলছেন। যে কেউ ঢুকে আবার বেরিয়ে যেতে পারে, চোখেও পড়বে না ঢুলুনিতে আচ্ছন্ন রক্ষীর। শুধু মূল গেটটা টপকাতে হবে। যেটা কোনও ব্যাপারই নয় মোটামুটি শারীরিক সক্ষম যে কারও পক্ষে।
এই যখন অবস্থা, কী করে পুরোপুরি ভরসা করা যায় এদের কথায়? কী করে একশো শতাংশ নিশ্চিত হওয়া যায়, ২৯ তারিখ অন্য কোনও বহিরাগত যাননি লীনার ফ্ল্যাটে, মিস্টার সেন ছাড়া? এরা কিছু বললেই ‘ভিজিটর্স রেজিস্টার’ দেখাচ্ছে। সব ওতে নোট করা থাকে।
কী নোট করা থাকে, খুঁটিয়ে দেখতে গিয়েই ঘোরতর খটকা। এটা কী হল? ২৯ তারিখ দুপুর সোয়া দুটোয় মিস্টার সেন এসেছিলেন, এন্ট্রি আছে। কিন্তু চারটে থেকে সাড়ে ছ’টার মধ্যে দুটো এন্ট্রি পড়া যাচ্ছে না। জলে ধুয়েমুছে গেছে, হাজার চেষ্টাতেও উদ্ধার করা যাচ্ছে না নাম দুটো। আগে-পরের দিনগুলো নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। শুধু খুনের দিন এবং সম্ভাব্য সময়ের এন্ট্রিতেই জল পড়ে গেল? কী করে?
বৈদ্যনাথের একেবারেই মনঃপূত হল না কেয়ারটেকার দিলীপবাবুর ব্যাখ্যা, ‘সেদিন সারাদিন ধরে বৃষ্টি হয়েছিল। ভিজিটর্স রেজিস্টার বেশিরভাগ সময় তো বাইরেই থাকে। বৃষ্টির জল অসাবধানে পড়েই হয়তো এন্ট্রিগুলো…।’ শুধু ওই দিনের, ওই সময়েই বৃষ্টিজল? বৈদ্যনাথ রেজিস্টার নিয়ে গেলেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের কাছে। ওঁরাও পারলেন না মুছে যাওয়া নামগুলো পড়তে।
বেশ, নাম না হয় পড়া যাচ্ছে না। মাত্র তো দিনকয়েক আগের কথা, মনে করে দেখুন না, মিস্টার সেনের পর আর কে কে এসেছিলেন বাইরে থেকে? ২৯ তারিখ দুপুর চারটে থেকে সন্ধে সাড়ে ছ’টার মধ্যে? লিফটম্যান বরুণ অনেক ভেবে জানালেন, দু’জন এসেছিলেন। একজন দাড়িওলা ভদ্রলোক, মাঝবয়সি। আরেকজন প্রৌঢ়া। কেউই লীনার ফ্ল্যাটে যাননি। প্রথমজন সাততলায় নেমেছিলেন, দ্বিতীয়জন পাঁচে। সঙ্গে বরুণ যোগ করলেন ‘যদ্দূর মনে পড়ছে।’
বরুণের ‘মনে পড়া’য় আস্থা রাখার কোনও কারণ পাচ্ছিলেন না বৈদ্যনাথ। যদি আস্থা রাখেনও তর্কের খাতিরে, বহিরাগত কেউ তো অন্য ফ্ল্যাটের নম্বর এন্ট্রি করে, অন্য তলায় নেমে আরামসে যেতেই পারে লীনার ফ্ল্যাটে। কে দেখতে যাচ্ছে? লিফটে কে কোন তলায় নেমেছিলেন, কী প্রমাণ হয় তাতে?
.
তিন সপ্তাহ পেরিয়ে গেছে খুনের পর। প্রমাণ বা সূত্র মেলেনি কিছু খুনিকে চিহ্নিত করার মতো। এদিকে প্রায়ই সিপি খোঁজ নিচ্ছেন, কিছু হল কিনা? অবসন্ন লাগে বৈদ্যনাথের। সন্ধেবেলায় গেলেন ডিসি ডিডি-র ঘরে। গুরুত্বপূর্ণ মামলায় তদন্তকারী অফিসারকে দৈনন্দিন হালহকিকত জানাতে হয় গোয়েন্দাপ্রধানকে। নিয়ম।
শ্রান্ত চেহারাটা দেখেই গোয়েন্দাপ্রধান বোঝেন, নির্ণায়ক সূত্র এখনও অধরা থাকায় হতাশা ক্রমশ ঘিরে ধরছে বৈদ্যনাথকে। পিঠে হাত রাখেন, ‘লেগে থাকাটাই আসল। দরকারে শূন্য থেকে শুরু করো। দেখবে, হঠাৎ লিড পেয়ে যাবে। ছেড়ো না। লেগে থাকো।’
ঠিকই। লেগে থাকতে হয়। গাভাসকার একবার বলেছিলেন, যে-কোনও পেশায় সফল হতে গেলে তিনটে ‘ডি’ প্রয়োজন। ডিসিপ্লিন, ডেডিকেশন, ডিটারমিনেশন। শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা, সংকল্প। সফল তদন্তকারীর অবশ্য সবার আগে দরকার তিনটে ‘পি’। পেশেন্স, পেশেন্স এবং পেশেন্স। অনন্ত ধৈর্য সর্বাগ্রে। মেধা-পরিশ্রম-একাগ্রতা, এসব আসবে অনেক পরে। ধৈর্যই তদন্তকারীর আসল চাঁদমারি। কিছুতেই যখন কিছু হচ্ছে না, নিজেকেই বারবার গুনগুনিয়ে ‘হাল ছেড়ো না বন্ধু’ শুনিয়ে যাওয়া চেতনে-অবচেতনে।
পরের দিন অফিসে এসে শূন্য থেকেই ফের শুরু করেন বৈদ্যনাথ। সন্দেহের বৃত্ত খুব বড় নয়। সন্দেহভাজনের তালিকায় শীর্ষবাছাই নিঃসন্দেহে প্রদীপকুমার সেন। সম্ভাব্য মোটিভ? দাম্পত্য অশান্তির সহ্যসীমা অতিক্রম করা। সম্পর্ক যে তিক্ত থেকে তিক্ততর হয়েছিল, উল্লেখ আছে লীনার ডায়েরিতে। টাকাপয়সা নিয়ে অশান্তি কি চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল? লীনার বন্ধুমহল থেকে জানা যাচ্ছে, শহরের প্রথম সারির বিউটি পার্লারগুলোয় নিয়মিত যাতায়াত ছিল। দিনে তিন-চার প্যাকেট ক্ল্যাসিক সিগারেট খেতেন। অভ্যস্ত ছিলেন মদ্যপানে। চাকরি করতেন না, স্বামীর দেওয়া মাসিক তিন হাজারে চলত কী করে এতসব? অন্য উপার্জন ছিল? থাকলে, কী তার উৎস? কে টাকা দিত, এবং কেন? অন্য পুরুষসঙ্গ, এক বা একাধিক? প্রদীপ জেনে গিয়েছিলেন? যৌন-ঈর্ষা?
অন্যদিকে, খুনের দিনের গতিবিধি সম্পর্কে প্রদীপের বয়ান মিলে যাচ্ছে লিফটম্যান-কেয়ারটেকারের বিবরণের সঙ্গে। আনুমানিক যে সময়ে খুন বলে চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, প্রদীপ সেই সময়সীমার মধ্যে লীনার ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন। সর্বসমক্ষেই গিয়েছিলেন। তাজ বেঙ্গলে খোঁজ নিয়ে জানা যাচ্ছে, সত্যিই সেদিন লাঞ্চ বুকিং ছিল সেনদম্পতির। এবং সে-রাতে সত্যিই ফোন ডেড হয়ে গিয়েছিল লীনার মায়ের বাড়িতে। নিজে মহিলার সঙ্গে কথা বলে জেনেছেন বৈদ্যনাথ। ফোলিও ব্যাগে কী ছিল? উত্তরে বলেছেন, অফিসের কাগজপত্র। হতেই পারে। অবিশ্বাসের কোনও কারণ নেই। সর্বোপরি নিজেই লালবাজারে এসে খোদ নগরপালের সঙ্গে দেখা করে তদন্তপ্রক্রিয়া চালু করেছেন প্রদীপ। না হলে তো স্রেফ ‘মিসিং ডায়েরি’-র অনুসন্ধানেই সময় চলে যেত রুটিনমাফিক। কিছুই তো সেভাবে লুকোনোর চেষ্টা করেননি, বৈবাহিক অশান্তির তীব্রতাটা বাদ দিয়ে।
অবশ্য সম্ভাব্য অপরাধীর এই ‘কিছুই তো লুকোচ্ছি না’-র প্রবণতা নতুন কিছু নয়। অনেকই হয়। পুলিশকে বিপথে চালিত করতে সব তাস আগেভাগেই দেখিয়ে দেওয়ার চালাকি, যাতে সন্দেহের সূচিমুখ একটা সময়ের পর ধাবিত হয় অন্য দিকে। আর এ তো কল্পনার গোয়েন্দাকাহিনি বা সিনেমা নয়, যে পুলিশ যাকে প্রাথমিক তদন্তে অপরাধী মনে করছে, শেষ বিচারে তার দোষী হওয়ার সম্ভাবনা শূন্য। এ তো ‘ফিকশন’ নয়, যে কোনও মহাপ্রতিভাধর গোয়েন্দা মধ্যপথে আবির্ভূত হবেন এবং শেষে পুলিশি ধারণাকে দুরমুশ করে ছাড়বেন। এবং দেখা যাবে, পুলিশ যা ভেবেছিল, সবই স্থূলবুদ্ধির প্রতিফলন মাত্র। সুতরাং প্রদীপ সেনকে ক্লিন চিট দেওয়াটা আহাম্মকি হবে। কিন্তু যদি প্রদীপ খুনটা করে থাকেন, প্রমাণ কই? সন্দেহের বশে তো আর খুনের মামলায় কাউকে আদালতে চালান করা যায় না, যখন ন্যূনতম প্রমাণটুকুও নেই হাতে। আর যদি প্রদীপ খুনি না হন, তা হলে কে? অন্য কেউ? না, অন্য কারা?
‘অন্য কেউ’ বলতে ডাক্তার স্বয়ম্ভু মুখার্জির নাম মাথায় আসতে বাধ্য। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে, সন্দেহের আওতার বাইরে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? হ্যাঁ, ‘অ্যালিবাই’ যথেষ্ট মজবুত। খুনের দিনে, খুনের সম্ভাব্য সময়ে বাড়িতেই ছিলেন, যাচাই করে জানা গিয়েছে নিঃসংশয়। কিন্তু এমনও তো হতে পারে, খুনটা নিজে করেননি। করিয়েছেন। মোটিভ তো ছিলই। ফ্ল্যাটের দখল ফিরে পাওয়া এবং নতুন করে ভাড়া দেওয়া বা বেচে দেওয়া। অমন জায়গায় ফ্ল্যাট অনায়াসে বিক্রি হবে বিশাল অঙ্কের টাকায়। ভাড়া দিলেও পাবেন, লীনা যা দিতেন, তার অন্তত তিনগুণ।
ফ্ল্যাটের প্রসঙ্গেই কিছু খটকা। লীনার জীবনযাপন নিয়ে যে তাঁর সঙ্গে এত বিশ্রী কাদা ছোড়াছুড়ি হয়েছিল, এটা প্রাথমিক কথাবার্তায় চেপে গেলেন কেন? মামলা নিয়ে কোনও আপসরফা হয়েছিল লীনার সঙ্গে? হলে কেমন রফা? কী সেই রফাসূত্র?
সম্পর্কের উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও খুনটা যদি স্বয়ম্ভুই লোক লাগিয়ে করিয়ে থাকেন, ধরে নিতে হয়, ফ্ল্যাটের মালিকানা প্রাপ্তি কারণ হিসাবে নেহাতই গৌণ। গভীরতর উদ্দেশ্য ছিল কিছু। কী হতে পারে? ‘সম্পর্কের উন্নতি’ মানে কী? কেমন সম্পর্ক? সেই সূত্রেই ব্ল্যাকমেল? বা আরও গুরুতর কিছু? হাজার প্রশ্ন মাথায় ঘুরতে থাকে বৈদ্যনাথের।
খুনটা করানোই যদি হয়ে থাকে, তা হলে কাদের দিয়ে? আবাসনের কর্মীদের এক বা একাধিককে দিয়ে করানোটাই সবচেয়ে সহজ। ফ্ল্যাটের অ-আ-ক-খ থেকে অনুস্বার-চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত নখদর্পণে ওদের। টাকার লোভ বড় সাংঘাতিক জিনিস। হতেই পারে, টাকার বিনিময়ে নিরাপত্তাকর্মীদের কয়েকজনকে, বা হয়তো একজনকেই, হাত করে খুনটা করিয়েছেন স্বয়ম্ভু।
সম্ভাবনা নম্বর তিন, খুনটা স্রেফ ব্যক্তিগত আক্রোশের বশে হয়েছে। এবং করেছেন আবাসনের এক বা একাধিক কর্মী। লীনা মিষ্টভাষী ছিলেন, এমন অভিযোগ জেরার সময় আবাসনের কেউ করেননি। অত্যন্ত রগচটা ছিলেন। মুখে কোনও লাগাম থাকত না রেগে গেলে। বৈদ্যনাথ বিশ্বস্ত সোর্স লাগিয়েছিলেন একাধিক। যারা নানা কাজকর্মের ছুতোয় ভাব জমানোর চেষ্টা করেছে মৈনাক-এর কর্মীদের সঙ্গে। এবং সোর্স মারফত পাওয়া খবর অনুযায়ী, ঘটনার দিনদশেক আগে লিফটম্যান বরুণের সঙ্গে তীব্র বাদানুবাদ হয়েছিল লীনার। লিফট খুলতে দেরি হয়েছিল। যাচ্ছেতাই ভাষায় গালাগালি করেছিলেন লীনা। সে নিয়ে কেয়ারটেকার অফিসে নাকি চর্চাও হয়েছিল বিস্তর।
লীনা নাকি মানুষ বলেই গণ্য করতেন না কর্মীদের, এতটাই নাকউঁচু ছিলেন। কর্মীরাও অত্যন্ত অপছন্দ করতেন বদমেজাজি লীনাকে। পুষে রাখা রাগ জমতে জমতে কি কোনওভাবে এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, যে একক বা যৌথ ষড়যন্ত্রে একেবারে মেরে ফেলারই সিদ্ধান্ত? ভাবতে একটু কষ্টকল্পিত লাগলেও একেবারেই অসম্ভব কি? আর সবচেয়ে বড় কথা, বৃষ্টির জলে শুধু সেদিনের ওই সময়ের এন্ট্রি দুটোই মুছে গেল? একটু বেশিই কাকতালীয় না?
একটাই দূরতম সম্ভাবনা পড়ে আছে আর। বব শেষাদ্রি। লীনার প্রথম স্বামী। যাঁর কোনও খোঁজই পাওয়া গেল না এদিক-ওদিক অনেক খবর নিয়েও। কেউ কিছু বলতে পারলেন না। এই বব কি কোনওভাবে ফের উদয় হয়েছিলেন লীনার জীবনে? হলেই বা কী, সন্ধান তো পেতে হবে আগে।
আর এমনই কপাল, না লীনা-প্রদীপ, না স্বয়ম্ভু, কেউই ব্যবহার করতেন না মোবাইল। চার বছর আগে, ’৯৫-এ, ভারতে এসে গিয়েছে মোবাইল ফোন। রাস্তাঘাটে সবারই হাতে হাতে ফোনের অভ্যেস চালু হতে তখনও ঢের দেরি। তবু, সামাজিক অবস্থানের বিচারে ওঁদের তিনজনের কাছে থাকতেই পারত মোবাইল। থাকলে তদন্তে সুবিধে হত অনেক। যাক, ছিল না যখন, কী আর করা?
ঘটনার পরের দুই সপ্তাহে প্রদীপ-স্বয়ম্ভু তো বটেই, আবাসনের কর্মীদের সবাইকে লালবাজারে ডেকে দফায় দফায় জেরা করেছেন বৈদ্যনাথ। অন্তত চারবার তো বটেই। তবু সিদ্ধান্ত নিলেন সবাইকে আর একবার তলব করার। পঞ্চমবার রুটিনমাফিক ডেকে পাঠানোর সময় জানতেন না, রহস্যভেদ দ্রুত হতে চলেছে অভাবিত ঘটনাপ্রবাহে।
২৯ জুলাই। লালবাজারের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের দোতলা। ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা। সকাল দ্রুত পা চালাচ্ছে দুপুরের দিকে। নিজের ঘরে আছেন বৈদ্যনাথ। সঙ্গে এক সহকারী অফিসার। পাশের একটা ঘরে অপেক্ষায় প্রদীপকুমার সেন, ডা. স্বয়ম্ভু মুখার্জি, মৈনাক-এর কেয়ারটেকার দিলীপ আর লিফটম্যান বরুণ। দিলীপ-বরুণ ফিরে গেলে বাকিদের আসার কথা পালা করে।
প্রথমে প্রদীপ। বৈদ্যনাথ ইচ্ছে করেই সবাইকে বসিয়ে রেখেছেন ঘণ্টাখানেক। মিস্টার সেনের ডাক পড়ল প্রায় পৌনে একটায়। এত দেরি হওয়ায় বেশ ধৈর্যচ্যুত দেখাচ্ছে ভদ্রলোককে। বিরক্তি গোপনের চেষ্টাও করলেন না বিশেষ। চেয়ার টেনে বৈদ্যনাথের মুখোমুখি বসতে বসতেই বললেন, ‘মিস্টার সাহা, এই নিয়ে পাঁচবার হল। একই কথা আর কতবার জানতে চাইবেন আপনারা? এক মাসও হয়নি আমার স্ত্রী মারা গেছেন। মেন্টালি ভীষণ ডিস্টার্বড আছি। অফিসের কাজও শিকেয় উঠেছে। তার মধ্যে বারবার লালবাজারে এভাবে আসতে হলে…।’
বৈদ্যনাথ স্ট্র্যাটেজি ঠিক করেই রেখেছিলেন। শুরু থেকেই চালিয়ে খেলবেন আজ। একদম কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তের স্টাইলে।
—সরি মিস্টার সেন। আমারই কি ভাল লাগছে বারবার এভাবে ডাকতে? আপনারা কেউই পুরো সত্যিটা বলছেন না বলেই ডাকতে হচ্ছে। উপায় কী?
প্রদীপও ঝাঁঝিয়ে উত্তর দেন।
—কোন সত্যিটা বলিনি? কোনটা?
বৈদ্যনাথকে এবার উত্তেজিত দেখায় সামান্য।
—আমাকে বলে দিতে হবে, কোনটা? ডায়েরির মাত্র কয়েকটা পাতা নিয়ে আপনাকে প্রশ্ন করেছি এতদিন। বাকিগুলোর কথা তুলিইনি। এই ভেবে, যে আপনি নিজেই বলবেন হয়তো।
টেবিলে রাখা লীনার ডায়েরিটা হাতে তুলে নিয়ে বলে চলেন বৈদ্যনাথ।
—খুন হওয়ার দিনতিনেক আগে আপনার মিসেস কী লিখেছিলেন ডায়েরিতে, শুনবেন?
‘এভাবে আর পারছি না আমি। সিঙ্গাপুরে গিয়ে আমাকে হোটেলের রুমের মেঝেতে শুতে বাধ্য করল প্রদীপ। আমার সঙ্গে বেড শেয়ার করতে নাকি ওর ঘেন্না করে। আমি নাকি রাস্তার মেয়ে। একটা সামান্য পারফিউম কিনতে চেয়েছিলাম গতকাল। মুখের উপর বলল, একটা পয়সাও খরচ করবে না আমার জন্য। বিদেশে বেড়াতে এনেছে, এই ঢের।’
একটু থামেন বৈদ্যনাথ, শান্ত ভাবে চোখে চোখ রাখেন প্রদীপ সেনের।
—কী সেনসাহেব, আরও শুনবেন? আমি আরও বলতে পারি। কিন্তু শুনতে আপনার ভাল লাগবে না…
প্রদীপ সেনের চোখমুখ এতক্ষণে রাগে থমথমে। থামিয়ে দেন প্রশ্নকারীকে।
—না, ভাল লাগছেও না। আর শুনতেও চাই না আমি। কারণ, লীনা চিরকালই মিথ্যেবাদী ছিল, ড্যাম লায়ার! শুনুন মিস্টার সাহা, পুরোটাই মিথ্যে ছিল ওর…
—কোনটা মিথ্যে? এই ডায়েরির লেখাগুলো মিথ্যে? টাকাপয়সা দিতেন না, জামাকাপড় দিতেন না, প্রতি মুহূর্তে অপমান করতেন, এগুলো মিথ্যে? সিঙ্গাপুরে একটা পারফিউম কিনতে চেয়েছিলেন বলে পাঁচটা কথা শুনিয়েছিলেন, মিথ্যে?
—দিতাম না, বেশ করতাম। আমার কাছে সাদা হাতি পোষার মতো হয়ে গিয়েছিল লীনা। টাকা, টাকা আর ওনলি টাকা। আমি তো তবু ওর শখ মেটাতে এতগুলো টাকা খরচ করে সিঙ্গাপুর নিয়ে গিয়েছিলাম। অন্য কেউ হলে করত না। আর পারফিউম, জামাকাপড়? ওর সবকিছু, এমনকী মৈনাক-এ যে আন্ডারগার্মেন্টস পরে গিয়েছিল সেদিন, সেগুলোও সিঙ্গাপুরের lingerie shop থেকে কেনা।
শেষ বাক্যটা বলেই আচমকা থেমে যান প্রদীপ। দৃশ্যতই অপ্রস্তুত। বৈদ্যনাথ নিমেষে বোঝেন, অপরাধীর যুক্তি-তক্কো-গপ্পোর বাসরঘরে এই সেই কাঙ্ক্ষিত ছিদ্র, যা নজরে আসা মাত্রই কালসর্প হয়ে ঢুকে পড়তে হয় তদন্তকারীকে, বিন্দুমাত্র কালবিলম্ব না করে।
—তাই? কী করে জানলেন ওই আন্ডারগার্মেন্টস পরেই সেদিন নিজের ফ্ল্যাটে গিয়েছিলেন লীনা? আধঘণ্টা থেকে কথাবার্তা বলেই তো চলে এসেছিলেন। ওটাই আপনার সঙ্গে শেষ দেখা, শেষ কথা। ওই সময়ের মধ্যে শারীরিক মিলন না হয়ে থাকলে নিশ্চিত হচ্ছেন কী করে অন্তর্বাসের ব্যাপারে? হয়েছিল?
স্রেফ ঢিল ছুড়েছিলেন বৈদ্যনাথ, একরকম মরিয়া হয়েই। যেটা পড়ে শুনিয়েছিলেন ডায়েরি থেকে, সেটা বানানো। সিঙ্গাপুরের ব্যাপারে কোনও এন্ট্রিই ছিল না ডায়েরিতে। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে আত্মঘাতী মন্তব্য করে বসবেন প্রদীপ, তিন সপ্তাহের দুর্ভেদ্য রক্ষণকে ভঙ্গুর দেখাবে রাতারাতি, ভাবতে পারেননি বৈদ্যনাথ। ক্রমশ অসহায় দেখাতে থাকে প্রদীপকে, আমতা-আমতা করে কিছু বলতে চেষ্টা করেন।
—না মানে…
—মানে একটাই হয় মিস্টার সেন। আপনি উকিল-টুকিলকে ফোন করতে পারেন। কোনও অসুবিধে নেই। আপনাকে অ্যারেস্ট করা হচ্ছে। সারা দিন সারা রাত পড়ে আছে। তবে যত তাড়াতাড়ি সত্যিটা স্বীকার করবেন, ততই ভাল। পুলিশি আদরযত্নের প্রয়োজন হবে না, আই অ্যাম শিয়োর। তা ছাড়া আপনার বয়স হয়েছে…
বৈদ্যনাথের গলার স্বর আমূল পালটে গিয়েছে এখন। এ স্বর প্রতিপত্তিশালী কর্পোরেট কর্তাকে সৌজন্যমিশ্রিত পুলিশি প্রশ্নের নয়। জালে জড়িয়ে যাওয়া অপরাধীকে উদ্দেশ করে এ স্বর এখন আত্মবিশ্বাসী আইনরক্ষকের। সব খুলে বলা ছাড়া উপায় ছিল না প্রদীপের।
পুরোটাই ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনা। সিঙ্গাপুরে বেড়াতে যাওয়ার আগেই। দুটো কারণ ছিল। এক, লীনার টাকাপয়সার বায়নাক্কা সামলাতে সামলাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন প্রদীপ। মুক্তির পথ খুঁজছিলেন। দুই, বিয়ের বছরদুয়েক পর থেকেই লীনার ‘কুছ পরোয়া নেহি’ জীবনযাপন। কখন কোন ক্লাবে কোন পুরুষের ঘনিষ্ঠ হচ্ছেন, কোন পার্টি থেকে কখন বেরিয়ে পুরুষসঙ্গীকে নিয়ে চলে যাচ্ছেন মৈনাক-এর ফ্ল্যাটে, খবর ঠিকই পেয়ে যেতেন প্রদীপ। সামাজিক পরিচিতির পরিধিটা নেহাত ছোট ছিল না তাঁর। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া ছিল প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক। লীনা বদলাননি নিজেকে, প্রদীপও আর্থিক দিক থেকে স্ত্রীকে কোণঠাসা করার চেষ্টা করেছেন ক্রমশ। এবং একটা সময় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন স্ত্রী-কে পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দেওয়ার।
সিঙ্গাপুরে বেড়াতে যাওয়াটা লোক-দেখানো। সপ্তাহদুয়েক আগেই যিনি স্ত্রী-র সঙ্গে বিদেশ ঘুরে এলেন, তিনি হঠাৎ খুন করতে যাবেন কেন সহধর্মিণীকে, এই ধারণা তৈরি করতে। তাজ বেঙ্গল-এ লাঞ্চের বুকিং-ও একই কারণে। স্ত্রী-র সঙ্গে যাঁর লাঞ্চে যাওয়ার কথা হয়ে আছে, তিনি সেদিনই খুন করবেন অক্লেশে, বিশ্বাসযোগ্য?
প্রদীপ প্রাথমিক জেরায় বলেছিলেন, কথা ছিল, লীনা বাড়ি থেকে ট্যাক্সিতে ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে আসবেন। মিথ্যে বলেছিলেন। কথা বরং ছিল, ফ্ল্যাটের তদারকিতে লীনা মৈনাক-এর ফ্ল্যাটে যাবেন। সেখানে পৌনে দুটো-দুটো নাগাদ প্রদীপ চলে আসবেন অফিস থেকে। লীনাকে তুলে লাঞ্চ করতে যাবেন একসঙ্গে।
প্রদীপ এসেছিলেন কথামতো, সময়মতো। হাতে ছিল ফোলিও ব্যাগ। যার ভিতরে ছিল কাপড়ের টুকরো, প্লাস্টিকের ছোট প্যাকেট একটা আর নারকেল দড়ি। লীনার ফ্ল্যাটে গিয়ে টুকটাক কিছু কথাবার্তার পর আচমকাই আক্রমণ করেছিলেন স্ত্রী-কে। প্রদীপ, আগে লিখেছি, যথেষ্ট স্বাস্থ্যবান ছিলেন। হতচকিত লীনার সাময়িক প্রতিরোধকে আয়ত্তে আনতে বেশি সময় লাগেনি। শ্বাসরোধ করে মেরেছিলেন স্ত্রী-কে। তারপর বিবস্ত্র করে দিয়েছিলেন লীনাকে। এটা কেন? প্রদীপের মুখেই শুনুন— ‘রাগে। ওকে সবার সামনে লিটারালি বেআব্রু করে দিতে চেয়েছিলাম। অনেকে তো জানতই ওর চরিত্রের স্বরূপ। এবার দেখুক। সবাই দেখুক।’
রান্নাঘরে লীনার দেহ ঢুকিয়ে রেখে বেরিয়ে এসেছিলেন প্রদীপ। মুখে কাপড় গুঁজে, হাত নারকেল দড়ি দিয়ে বেঁধে। ফোলিও ব্যাগে ভরে নিয়েছিলেন লীনার পোশাকআশাক আর হ্যান্ডব্যাগ। হ্যান্ডব্যাগ থেকে ফ্ল্যাটের চাবিটা নিয়ে বাইরে থেকে তালা বন্ধ করে লিফট ডেকেছিলেন নির্বিকার। আবাসন থেকে বেরিয়ে অফিস ফেরার পথে ড্রাইভার ইসমাইলকে বলেছিলেন আউট্রাম রোড হয়ে যেতে। গাড়িটা দাঁড় করিয়েছিলেন নেচার পার্ক-এর সামনে। ইসমাইল অপেক্ষা করছিল গাড়িতে, আর প্রদীপ ব্যাগ হাতে ঢুকে গিয়েছিলেন পার্কে। চাবিটা একটা প্লাস্টিকের প্যাকেটে মুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন ঝোপঝাড়ের মধ্যে। লীনার জামাকাপড় ব্যাগসুদ্ধ ফেলেছিলেন আর-এক প্রান্তে। তারপর সোজা অফিস। পরের দিন থানায় ডায়েরি, আর তারও পরের দিন সশরীরে লালবাজারে এসে কুম্ভীরাশ্রু। পচাগলা মৃতদেহ কয়েকদিনের মধ্যে আবিষ্কৃত হবেই, জানতেন প্রদীপ। প্রশ্নের জবাব দেওয়া তখন মুশকিল হবে, জানতেন। তাই এগিয়েছিলেন আটঘাট বেঁধেই।
স্বীকারোক্তি অনুযায়ী যাওয়া হল নেচার পার্ক-এ। কাগজের মোড়কে চাবিটা পাওয়া গিয়েছিল নির্দিষ্ট জায়গাতেই। কিন্তু পাওয়া যায়নি লীনার পোশাক আর হ্যান্ডব্যাগ। কত লোকেরই তো যাতায়াত ওই পার্কে নিত্যদিন। কেউ হয়তো নিয়ে গিয়েছিল দেখতে পেয়ে।
চার্জশিটের প্রস্তুতি যখন তুঙ্গে, তখনও বৈদ্যনাথ পাননি একটা প্রশ্নের উত্তর। খুনের দিন ‘ভিজিটর্স রেজিস্টার’-এ জলের দাগে দুটো এন্ট্রি মুছে যাওয়াটা। কী ব্যাখ্যা? উত্তর মেলেনি। এমন ব্যাখ্যাতীত সমাপতন বোধহয় কালেভদ্রেই সম্ভব, যা হাজির হয় তদন্তকে বিপথগামী করার সম্ভাব্য উপাদানসমেত।
এ মামলার পরিণতি অনেকাংশেই ছিল পারিপার্শ্বিক প্রমাণ (circumstantial evidence) নির্ভর। খুনের কোনও প্রত্যক্ষদর্শী নেই। শ্বাসরোধ করে হত্যা, খুনে ব্যবহৃত অস্ত্রের প্রশ্ন নেই। অকুস্থলের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় আঙুলের বা পায়ের ছাপ মেলেনি অভিযুক্তের। অপরাধী কে, সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে গেলেও তদন্তকারীকে অসম্ভব যত্নবান হতে হয় এ ধরনের মামলায়, যেখানে প্রমাণ-পরম্পরায় (chain of evidence) সামান্যতম ফাঁকফোকর থাকলেও ভরাডুবি অনিবার্য। এবং এ ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ছিলেন অর্থবান। প্রদীপকুমার সেন যে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে অর্থব্যয় করবেন যথেচ্ছ, জানাই ছিল।
কী ঘটেছিল, কীভাবে এবং কেন, চার্জশিটে উঠে এসেছিল ছবির মতো। বিচারপর্বে অভিযুক্তের আইনজীবীর প্রধান যুক্তি ছিল, ষাট বছরের এক প্রৌঢ়র পক্ষে একা ওইভাবে প্রায় পনেরো বছর কম বয়সের মহিলাকে খুন করা অসম্ভব। এ যুক্তি ধোপে টেকার ছিল না। টেকেওনি। লীনাকে কাবু করার মতো স্বাস্থ্য যে অভিযুক্তের ছিল, রায়ে উল্লিখিত হয়েছিল।
পারিপার্শ্বিক প্রমাণ হিসাবে প্রত্যাশিতভাবেই সর্বোচ্চ গুরুত্ব পেয়েছিল পার্ক থেকে উদ্ধার হওয়া চাবির গোছা। লীনার তালাবন্ধ ফ্ল্যাটের চাবি কী করে প্রদীপের কাছে এল, আর কেনই বা সেটা লুকিয়েচুরিয়ে ফেলে এলেন পার্কে, জবাব ছিল না এ প্রশ্নের। ড্রাইভার ইসমাইল তাঁর বয়ানে স্বীকার করেছিল পার্কে যাওয়ার কথা। পার্কের নিরাপত্তারক্ষীদের বয়ান নেওয়া হয়েছিল। একজন মনে করতে পেরেছিলেন সেদিনের কথা। গাড়ি এসে থেমেছিল, একজন ব্যাগ নিয়ে নেমেছিলেন, ফিরে এসেছিলেন কিছুক্ষণের মধ্যে খালি হাতে। এজলাসে প্রদীপকে চিহ্নিত করেছিলেন ওই রক্ষী।
কী পড়ে থাকে আর? লীনার ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ থাকা অসুখী দাম্পত্যের বিবরণ বিবেচিত হয়েছিল খুনের ‘মোটিভ’ হিসাবে। ডায়েরির হাতের লেখা যে লীনারই, চিহ্নিত করেছিলেন ভাই অমিত। সর্বোপরি, জীবিত অবস্থায় লীনাকে শেষ দেখা গিয়েছিল প্রদীপের সঙ্গে। দেখেছিলেন লিফটম্যান বরুণ, যখন প্রদীপ ফ্ল্যাটের বেল বাজিয়েছিলেন ২৯ তারিখ দুপুরে, লীনা খুলেছিলেন দরজা এবং প্রদীপ ঢুকে গিয়েছিলেন ফ্ল্যাটে। সাক্ষ্যপ্রমাণের ভাষায় একে বলে হয় ‘last seen alive together’, যা এই ধরনের মামলায় (যেখানে কোনও প্রত্যক্ষদর্শী নেই অপরাধের) প্রমাণ হিসাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আদালতের রায়ে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন প্রদীপকুমার সেন। দণ্ডিত হয়েছিলেন যাবজ্জীবন কারাবাসে। এখন পরলোকগত।
সম্পর্কের রসায়ন ভারী বিচিত্র। বিনিয়োগের রসায়ন। কোথাও পুঁজি স্রেফ বিশ্বাস, কোথাও-বা নির্ভরতা। কোথাও হয়তো ভালবাসা, কোথাও অন্য কোনও অনুভূতি। ঈর্ষা-ক্ষোভ-দ্বেষ, বা অন্য কিছু।
প্রদীপ-লীনার সম্পর্কেও বিনিয়োগ ছিল উভয়ত। অব্যক্ত হিসেব ছিল পারস্পরিক। নারীবিষয়ে প্রদীপের দুরারোগ্য দুর্বলতা লীনা বিলক্ষণ বুঝেছিলেন। এবং প্রৌঢ়ত্বের স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা প্রদীপকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিলেন একটাই কারণে। নিজে গভীর আসক্ত ছিলেন জেটগতির দিনযাপনে। সেই জীবনযাত্রায় অর্থবান এবং সামাজিক প্রতিপত্তিশালী স্বামী দীর্ঘস্থায়ী অনুঘটক হয়ে দেখা দেবেন, এই নিশ্চিন্ততায়।
আর প্রদীপ? রিপুর তাড়না চরিতার্থ করাই ছিল পাখির চোখ। ‘শরীর শুধু শরীর, তোমার মন নাই লীনা’ বলার কথা দুঃস্বপ্নেও ভাবেননি কখনও। বলবেন, এমন প্রত্যাশাও লীনার ছিল না।
প্রেম ছিল না ওঁদের। চাওয়া-পাওয়ার হিসেব ছিল। যা দু’জনেই ভালবাসার আব্রু দিয়ে ঢেকে রাখার চেষ্টা করেছিলেন বিয়ের পরের কয়েক মাস। কিন্তু যে সম্পর্কের ইট-বালি-চুন-সুরকিতে শুধুই দেওয়া-নেওয়া, তাতে ফাটল ধরা ছিল অবধারিতই। ‘কী পাইনি তার হিসাব মিলাতে’-ই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন উভয়েই।
পরিণতি? পড়লেন তো!
২.০৫ এ কাহিনির শিরোনাম হয় না
[বীরেশ পোদ্দার মামলা
পৃথ্বীরাজ ভট্টাচার্য, ইনস্পেকটর, গোয়েন্দাবিভাগ।]
ঠিক যেন ‘শোলে’! স্থান-কাল-পাত্রে দূরতম মিলও নেই। মিল নেই পটভূমিতেও। তবু মনে পড়ে যেতে বাধ্য রমেশ সিপ্পির কালজয়ী ব্লকবাস্টারের সেই দৃশ্য।
পাশাপাশি শোয়ানো পাঁচটি মৃতদেহ। সাদা কাপড়ে মোড়া। দীর্ঘদিন পর পাওয়া ছুটিতে দেশের বাড়ি ফিরছেন জাঁদরেল পুলিশ অফিসার সঞ্জীবকুমার, রামগড়ে নিজের গ্রামে যিনি সর্বজনমান্য ঠাকুরসাব। যিনি সদ্য গ্রেফতার করে জেলে পুরেছেন দুর্ধর্ষ ডাকাত গব্বর সিং-কে। স্টেশনে বাড়ির লোকজন নেই কেউ, দেখে অবাকই হয়েছেন। কেউ এল না? আশ্চর্য!
বাড়ি পৌঁছনোর পর বিস্ময় বদলে গেছে স্তব্ধতায়। পাতা পড়ছে না চোখের। পাশাপাশি পাঁচটি দেহ শুয়ে নিথর। দুই ছেলে, একমাত্র মেয়ে, পুত্রবধূ। এবং আট বছরের নাতি। জেল পালিয়ে যাদের খুন করে গেছে গব্বর, ভয়ংকরতম বদলা নিয়েছে গ্রেফতারির। পরিবার নিশ্চিহ্ন। অক্ষত শুধু ছোটছেলের স্ত্রী, আর বহু বছরের গৃহভৃত্য। যাঁরা গব্বরের হত্যালীলার সময় পুজো দিতে গিয়েছিলেন মন্দিরে।
গৃহভৃত্য কাঁদছেন মনিবের পা জড়িয়ে ধরে। ছোটবউ বাড়ির দালানে বসে আছেন শোকস্তব্ধ। এতদিন পরে বাড়ি আসছেন, পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জন্য ঠাকুরসাব কিছু-না-কিছু কিনে এনেছিলেন। দু”হাত থেকে খসে পড়তে থাকে সেই উপহারগুচ্ছ। একটার পর একটা।
দমকা হাওয়া আসে। উড়িয়ে নিয়ে যায় চারটি দেহের উপর থেকে সাদা কাপড়। তিন সন্তান এবং পুত্রবধূর গুলিবিদ্ধ দেহে একে একে চোখ রাখেন বাক্রুদ্ধ ঠাকুরসাব। পঞ্চম দেহের উপরের কাপড় তখনও উড়ে যায়নি হাওয়ায়। নাতির দেহের উপর থেকে নিজেই কাপড় সরান ধীরে। শোক ততক্ষণে বদলে গেছে উন্মত্ত ক্রোধে।
.
মুরারিপুকুরের দশ বাই বারোর একচিলতে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে ‘শোলে’ মনে পড়ে যায় ওসি মানিকতলার। বাহ্যত মিল নেই কোনও, তবু। ওটা সিনেমার পরদা, এটা ঘোর বাস্তব। ওটা ঘটেছিল খোলা আকাশের নীচে, এটা ঘটেছে চার দেওয়ালের মধ্যে। ওটায় ঘাতক ছিল বন্দুকের গুলি, এটায় গলার ফাঁস। রামগড়ে নিহতের সংখ্যা ছিল পাঁচ। এখানে মেঝেতে একটা, আর খাটের উপর পাশাপাশি পড়ে আছে পাঁচটা দেহ। ওটায় লাশগুলোর মুখ ঢাকা ছিল কাপড়ে। এখানে নেই।
মেঝেতে প্রাণহীন দেহ এক মহিলার। গলায় উলের চাদরের প্যাঁচ। বয়স তিরিশের নীচেই হবে। খাটে ফুলের মতো পাঁচটি বাচ্চা মেয়ে। যেন ঘুমোচ্ছে নিশ্চিন্তে। কারও গলায় ওড়নার ফাঁস, কারও গলায় মাফলারের। বয়স? সবচেয়ে বড় যে, সে কিছুতেই বারোর বেশি নয়। সবচেয়ে ছোট দু’জনকে দেখলেই বোঝা যাচ্ছে যমজ। বয়স খুব বেশি হলে পাঁচ-ছয়।
পুলিশের চাকরিতে কম দিন হল না মানিকতলা থানার বড়বাবু দ্বিজেন চ্যাটার্জির। অসংখ্য মৃতদেহ দেখেছেন। দুর্ঘটনায় ধড় থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া শরীর দেখেছেন অনেক। দুমড়ে-মুচড়ে দলা পাকিয়ে যাওয়া বডি দেখেছেন একাধিক। তদন্তের স্বার্থে বহুবার ডাক্তারবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে দেখেছেন ময়নাতদন্তের কাটাছেঁড়া। দেহ, সে যতই বিকৃত হোক, স্নায়ু বিন্দুমাত্রও চঞ্চলতা দেখায়নি কখনও।
সঙ্গী সাব-ইনস্পেকটর তাই অবাকই হন একটু। দ্বিজেন ঠায় তাকিয়ে আছেন পড়ে থাকা হাফডজন দেহের দিকে। একটু এগিয়ে যান যমজ মেয়েদুটির গলার ফাঁস পরীক্ষা করতে। মুখের উপর ঝুঁকে কয়েক সেকেন্ড দেখার পরই পিছিয়ে আসেন। ফ্যাকাশে হয়ে আসে চোখমুখ। অস্ফুটে অধস্তন সহকর্মীকে বলেন, ‘ডিসি ডিডি-কে ধরো।’ মোবাইল এগিয়ে দেন নিজের।
—স্যার, রিং হচ্ছে। ধরুন, ডিসি ডিডি সাহেব…
ফোন হাতে নিয়ে কোনওমতে ‘নমস্কার স্যার, এত রাতে ডিস্টার্ব করার জন্য সরি স্যার’ বলার পরই বিদ্রোহ করে বহুপরীক্ষিত স্নায়ু। হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেন ডাকসাইটে ওসি। জড়ানো গলায় শুধু বলতে পারেন, ‘একবার আসুন স্যার, শুধু দেখে যান, বাচ্চা মেয়েগুলোকে এভাবে… এতদিনের চাকরিতে এমন কখনও দেখিনি স্যার…।’
ঘড়ি দেখেন গোয়েন্দাপ্রধান। পৌনে চারটে। পোড়খাওয়া ওসি কীসে এতটা বিচলিত হয়ে পড়লেন, যে পুরো বাক্যটা শেষ করতে না পেরে কেঁদেই ফেললেন? এখনই যাওয়া দরকার স্পটে। বিছানা ছেড়ে উঠতে না উঠতেই মোবাইল বেজে উঠল আবার। এবার লালবাজার কন্ট্রোল রুম, ‘স্যার, মুরারিপুকুরে মাল্টিপল মার্ডার। ওসি স্পটে আছেন। ডিসি যাচ্ছেন। প্রবলেম হচ্ছে একটু। লোক জমে গেছে। বডি বার করতে সমস্যা হতে পারে। ডিসি হেডকোয়ার্টার স্পটে RAF পাঠাতে বলেছেন। ফোর্স যাচ্ছে স্যার।’
সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে ফোন কেটে দেন গোয়েন্দাপ্রধান, ‘হ্যাঁ, শুনেছি, ওসি-র সঙ্গে কথা হয়েছে। আমি যাচ্ছি। ওসি হোমিসাইডকেও যেতে বলুন। আর, পারলে সিপি সাহেবকে জানিয়ে রাখুন ইনসিডেন্টটা।’
গোয়েন্দাপ্রধানের গাড়ি যখন ঢুকছে মুরারিপুকুরে, ঘড়িতে ভোর সাড়ে চারটে। নাকি লেখা উচিত, রাত সাড়ে চারটে? সময়টাই এমন, যখন রাত আর ভোর সহবাস করে দৈনন্দিন।
.
রহস্যপিপাসুর সনাতন চাহিদা এ কাহিনি মেটাবে না, স্বীকার্য শুরুতেই। একটা অপরাধ ঘটবে, থাকবে একাধিক সন্দেহভাজন, প্রত্যেকেরই থাকবে অপরাধী হওয়ার সম্ভাব্যতা, পাঠক আগাগোড়া থাকবেন দ্বিধাদীর্ণ, আর গোয়েন্দা শেষ পৃষ্ঠায় যবনিকা উত্তোলন করবেন রহস্যের, এ কাহিনি এই পরিচিত ছকের অনুসারী নয়। বরং উলটো। শুরুতেই জানা হয়ে যাচ্ছে, কে খুনি। ‘কে করেছিল’ নয়, কেন করেছিল, এবং কীভাবে করেছিল, সেটাই উপজীব্য এ মামলার। যা আজও হিমশীতল নৃশংসতার বিরলতম দিকচিহ্ন হয়ে আছে কলকাতা পুলিশের ইতিহাসে।
মানিকতলা থানা, কেস নম্বর ৩৮২। তারিখ, ১৭ ডিসেম্বর, ২০০০। ধারা, ৩০২/৩০৭। খুন এবং খুনের চেষ্টা।
.
প্রণম্য শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘চিড়িয়াখানা’ উপন্যাসে এক জায়গায় লিখেছিলেন, ‘টেলিফোনের সহিত যাঁহারা ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত তাঁহারা জানেন, টেলিফোনের কিড়িং কিড়িং শব্দ কখনও কখনও ভয়ংকর ভবিতব্যতার আভাস বহন করিয়া আনে। যেন তারের অপর প্রান্তে যে-ব্যক্তি টেলিফোন ধরিয়াছে, তাহার অব্যক্ত হৃদয়াবেগ বিদ্যুতের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়।’
মানিকতলা থানায় যে ফোনটা এসেছিল রাত সোয়া তিনটে নাগাদ, তাতেও যেন আভাস ছিল ভয়ংকর ভবিতব্যের। ফোনের অন্য প্রান্ত থেকে এক হিন্দিভাষী ভদ্রলোক উত্তেজিত কণ্ঠে জানিয়েছিলেন ডিউটি অফিসারকে, ‘সার, জলদি ফোর্স ভেজিয়ে ইঁয়াহা। 16/J/Q মুরারিপুকুর রোড মে, ইয়াহাঁ পাঁচ লেড়কি অউর এক অউরত কা খুন হো গয়া।’ ভদ্রলোক যেখান থেকে ফোনটা করছেন, সেখানে যে পরিস্থিতি খুব একটা শান্ত নেই, কথোপকথনের মাঝেই ভেসে আসা চিৎকার-চেঁচামেচিতে দিব্যি বুঝতে পেরেছিলেন অফিসার।
থানার লাগোয়া কোয়ার্টারেই থাকেন ওসি। ঘণ্টাদেড়েক হল থানা ছেড়ে বাড়ি গেছেন। ডিউটি অফিসার ঘুম ভাঙালেন ফোনে, জানালেন খবরটা। ‘পাঁচ লড়কি অউর এক অউরত?’ অনেক উড়ো ফোন আসে থানায় রাতের দিকে। কিন্তু ছ’টা খুন? খবরটা ঠিক হোক, ভুল হোক, দেরি করার মানে হয় না। তৈরি হয়ে নিতে যতটুকু সময়, ওসি-র গাড়ি ছুটল মুরারিপুকুরের দিকে। এবং নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছেই দ্বিজেন বুঝলেন, খবরে ভুল নেই।
তিনতলা বাড়ি। তৃতীয় তলাটা অসম্পূর্ণ। ওই গভীর রাতেও অন্তত শ’তিনেক লোকের জমাট ভিড় বাড়ির গেটের সামনে। পুলিশের গাড়ি দেখেই যে ভিড়টা আরও উত্তেজিত হওয়ার অক্সিজেন পেয়ে গেল নিমেষে। কী হয়েছে, সেটা জানতে গেলে তো ঢুকতে হবে বাড়িতে। সেই ঢোকাটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল ভিড়ভাট্টা-হইহল্লার মধ্যে। বিস্তর ঠেলেঠুলে কোনওমতে বাড়িটায় ঢুকতে ঢুকতেই দ্বিজেন মোবাইল ফোনে ধরলেন লালবাজার কন্ট্রোল রুম। ‘সিচুয়েশন গ্রেভ অ্যাট মুরারিপুকুর। রিইনফোর্সমেন্ট নিডেড আর্জেন্টলি। প্লিজ় ইনফর্ম সিনিয়র অফিসার্স।’
একতলায় এগারোটা ঘর, দু’পাশে সার দিয়ে। জনাবিশেক লোকের ভিড় উত্তর দিকের শেষ ঘরের সামনে। ঘরের দরজা খোলা। সঙ্গী অফিসারকে নিয়ে দ্বিজেন ঢুকলেন। এবং ঢুকে যা দেখলেন, লিখেছি শুরুতেই। মেঝেতে এক মহিলার দেহ প্রাণহীণ, খাটে পঞ্চকন্যার। বিহ্বল ওসি কেঁদে ফেললেন দৃশ্যের অভিঘাতে, ‘বাচ্চা মেয়েগুলোকে এভাবে… এতদিনের চাকরিতে এমন কখনও দেখিনি স্যার…!’
ডিসি ইএসডি (ইস্টার্ন সাবার্বান ডিভিশন) এবং ডিসি ডিডি যখন এসে পৌঁছলেন, ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছেন দ্বিজেন। খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছেন দশ বাই বারোর ঘরটা। সহজেই চোখে পড়েছে জানালার পাশে রাখা একটা কাগজের টুকরো। আঁকাবাঁকা হাতের লেখায় যা ছিল সেই কাগজে, তুলে দিলাম নীচে।
‘হাম বীরেশ পোদ্দার আপনি ইচ্ছা সে পুরে পরিবার কো মার ডালা। ইস মে বাকি লোগো কা কোই কসুর নেহি হ্যায়। কৃপয়া সাজা দে, মারনে কা কারণ দিগ্বিজয় শর্মা কা মেরি পরিবার ইয়ানি মেরি বিবি সে গলত সম্পর্ক।’
(‘আমি বীরেশ পোদ্দার নিজের ইচ্ছেয় আমার পুরো পরিবারকে মেরে ফেলেছি। এতে অন্য কারও কোনও দোষ নেই। আমাকে শাস্তি দেওয়া হোক। মারার কারণ হল দিগ্বিজয় শর্মার সঙ্গে আমার স্ত্রী-র অবৈধ সম্পর্ক।’)
কাগজের নীচে ইংরেজিতে সই, ‘Biresh Poddar’। তা এই বীরেশ কই? বউ-বাচ্চাদের মেরে স্বীকারোক্তি লিখে পালিয়েছেন? যাঁরা ভিড় জমিয়েছিলেন ঘরের সামনে, তাঁরা সমস্বরে হইহই করে উঠলেন, ‘দিগ্বিজয় কো মারকে ভাগ গয়া!’
ঘটনাপ্রবাহ যা জানা গেল, এরকম। একতলায় এগারোটা ঘরের মধ্যে দশটায় ভাড়া থাকতেন সব মিলিয়ে সাতটি পরিবার। একটা ঘর খালি ছিল। উত্তর দিকের দুটো মুখোমুখি ঘরে ভাড়া থাকতেন বীরেশ পোদ্দার এবং দিগ্বিজয় শর্মা। বছর চল্লিশের বীরেশ আদতে বিহারের বাসিন্দা। বড়ভাই নরেশের সঙ্গে জীবিকার সন্ধানে কলকাতায় চলে আসেন বছর পনেরো আগে। দুই ভাই মিলে ক্যানাল ওয়েস্ট রোডে একটা ছোট ঘর ভাড়া নিয়ে কাঠের কাজকর্মের কারবার শুরু করেন।
নরেশ সপরিবারে থাকেন উলটোডাঙার কাছে। আর বীরেশ মুরারিপুকুরের এই বাড়ির ভাড়াটিয়া কলকাতায় আসার পর থেকেই। স্ত্রী রীতা এবং পাঁচ কন্যাকে নিয়ে বসবাস। রিমা-প্রীতি-স্মৃতি-ভাবনা-শ্বেতা। রিমা বড়, এগারো বছর। প্রীতি আর স্মৃতি মেজো আর সেজো, যথাক্রমে দশ আর আট বছরের। ভাবনা আর শ্বেতা যমজ, চার পেরিয়ে সবে পাঁচ ছুঁয়েছে।
প্রতিবেশী দিগ্বিজয় শর্মা মধ্যচল্লিশ। বড়বাজারের এক বেসরকারি সংস্থায় ছোটখাটো চাকুরে। বিবাহিত, একমাত্র ছেলে কৌশলের বয়স আঠারো। কলেজে পড়ে, বাবার সঙ্গেই থাকে। স্ত্রী থাকেন দেশের বাড়িতে, বিহারে।
একতলাতেই অন্য ঘরগুলোয় যাঁরা ভাড়া থাকতেন, তাঁদের মধ্যে দু’জন, সত্যদেও পাণ্ডে এবং রামচল জয়সওয়াল, জানালেন, রাত আড়াইটে নাগাদ বাইরে থেকে প্রবল চিৎকারে ঘুম ভেঙে যায় ওঁদের। প্যাসেজে সারারাতই আলো জ্বলত এ বাড়িতে। গেট বন্ধ হয়ে যেত সাড়ে এগারোটা নাগাদ। তালার কমন চাবি থাকত সব আবাসিকের কাছেই। কারও রাতে বেরনোর প্রয়োজন হলে তালা খুলে বেরতেন। ফিরে এসে গেট আবার তালাবন্ধ করে দিতেন।
দরজা খুলে বাইরে এসে সত্যদেও আর রামচল দেখেন, দিগ্বিজয় এক হাতে নিজের পেট চেপে ধরেছেন। রক্তে ভেসে যাচ্ছে শার্ট। আর অন্য হাতে কলার চেপে ধরে আছেন বীরেশের। দিগ্বিজয়ের ছেলে কৌশল তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, ‘পিতাজি কো মার ডালা!’ দিগ্বিজয়ের হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে ঝটিতি মূল গেট দিয়ে বেরিয়ে যান বীরেশ। গেট খোলা ছিল। নিশ্চয়ই বীরেশই খুলে রেখেছিলেন ঘটনা ঘটানোর আগে। যাতে দ্রুত পালাতে সুবিধে হয়।
দিগ্বিজয় কোথায়? সত্যদেও-রামচলের হইহইয়ে অন্য ভাড়াটেরাও বেরিয়ে এসেছিলেন। দু’তলায় থাকতেন বাড়ির মালিক শ্যামল সাহা, নেমে এসেছিলেন। দু’-তিনজন একটা ট্যাক্সি জোগাড় করে রক্তাক্ত দিগ্বিজয়কে নিয়ে ছুটেছিলেন আর জি কর হাসপাতালে। সেখানেই এখন আইসিইউ-তে চিকিৎসাধীন সে।
বীরেশের ঘরে বাইরে থেকে শিকল তোলা ছিল। শিকল খুলে ভিতরের ওই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে এক প্রতিবেশী ফোন করেছিলেন মানিকতলা থানায়।
অকুস্থল থেকে পুলিশের বাজেয়াপ্ত করা জিনিসের তালিকায় রইল হিন্দিতে লেখা বীরেশের স্বীকারোক্তি-চিরকুট, ঘরগুলির মধ্যবর্তী প্যাসেজে বইতে থাকা রক্তস্রোতের ‘স্যাম্পল’, দিগ্বিজয়কে আক্রমণে ব্যবহৃত ছুরি, এবং কিছু রুটিন টুকিটাকি।
দেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো দরকার। কিন্তু পারলে তো? সকাল হয়ে গেছে। লোকের ভিড় বেড়েছে আরও। পাঁচ-সাতশো এলাকাবাসীর বিক্ষুব্ধ জমায়েত বাড়ির সামনে। দাবি, এভাবে ছ’জনকে খুন করে পালিয়ে গেছেন বীরেশ, তাকে গ্রেফতার না করা পর্যন্ত একটাও দেহ বাড়ির বাইরে বেরবে না। আগে গ্রেফতার, তারপর অন্য কিছু।
সিনিয়র অফিসাররা জনতাকে আপ্রাণ বোঝানোর চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। ডিসি হেডকোয়ার্টার, যিনি শহরের আইনশৃঙ্খলার দায়িত্বে থাকেন, ততক্ষণে চলে এসেছেন লালবাজারে। মুরারিপুকুরে পৌঁছে গিয়েছে RAF। পরিস্থিতি ক্রমশ ঘোরালো হচ্ছে দেখে সামান্য বলপ্রয়োগ করতেই হল পুলিশকে। জনতাকে হঠিয়ে দিয়ে বার করা হল দেহগুলি। মৃতা মায়ের সঙ্গে পুলিশ ভ্যানে করে মর্গের উদ্দেশে রওনা দিল পাঁচ বোন। রিমা-প্রীতি-স্মৃতি-ভাবনা-শ্বেতা। ঘুমের মধ্যেই যারা কয়েক ঘণ্টা আগে পাকাপাকিভাবে পাড়ি দিয়েছে ঘুমের দেশে।
পোস্টমর্টেম রিপোর্ট জানাল, যা জানাই ছিল। ‘Death was caused due to effects of strangulation, ante-mortem and homicidal in nature.’
ঘটনা এতটাই চাঞ্চল্যকর, প্রাথমিক তদন্ত থানা শুরু করলেও গোয়েন্দাবিভাগের উপর দায়িত্ব পড়াটা অনিবার্যই ছিল। তদন্তকারী অফিসার নিযুক্ত হলেন গোয়েন্দাবিভাগের হোমিসাইড শাখার তৎকালীন সাব-ইনস্পেকটর পৃথ্বীরাজ ভট্টাচার্য, যিনি বর্তমানে গোয়েন্দাবিভাগেই কর্মরত ইনস্পেকটর হিসাবে।
প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেল, বীরেশ-রীতার দাম্পত্য সম্পর্ক মসৃণ ছিল না। ঝগড়াঝাঁটি লেগেই থাকত। রীতার পরিবারের লোকজন থাকতেন কাঁকুড়গাছি এলাকায়। রীতার দাদা চন্দ্রশেখর জানালেন, বীরেশ প্রায়ই মারধর করতেন রীতাকে। সন্দেহ করতেন, দিগ্বিজয়ের সঙ্গে বোধহয় স্ত্রীর অবৈধ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সন্দেহই, প্রমাণ ছিল না কিছু। মাঝেমাঝে রীতা রাগারাগি করে বাচ্চাদের নিয়ে চলে আসতেন দাদার বাড়িতে। কান্নাকাটি করতেন দাদা-বউদির কাছে।
কয়েকদিন পরে বীরেশই এসে ফিরিয়ে নিয়ে যেতেন স্ত্রীকে। রীতাও ফিরে আসতেন মুরারিপুকুরে। কী-ই বা উপায় ছিল ফিরে আসা ছাড়া? যখন কিশোরী ছিলেন, বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। পড়াশুনোর সুযোগ হয়নি। সম্পূর্ণভাবে স্বামীর উপর নির্ভরশীল ছিলেন। আর রীতার দাদা চন্দ্রশেখরও যে আর্থিকভাবে খুব সচ্ছল ছিলেন, এমনও নয়। পাঁচটা বাচ্চাকে নিয়ে কতদিনই বা থাকা যায় দাদা-বউদির সংসারে?
ফিরে আসতেন, কিছুদিন সব ঠিকঠাক চলত। তারপর ফের সন্দেহ, ফের অশান্তি, ফের মারধর। যথাপূর্বং তথাপরম।
নিশ্চিত জানা হয়ে গিয়েছিল, অপরাধী কে। বাকি ছিল গ্রেফতারি। বীরেশ সহজে ধরা দিলেন না। ভোগালেন সপ্তাহদুয়েক। ঘটনা ২০০০ সালের। মোবাইল ব্যবহার করার মতো ট্যাঁকের জোর ছিল না বীরেশের। তাই প্রযুক্তির সাহায্যে পলাতকের অবস্থান জানার প্রশ্ন ছিল না। বীরেশের ভাই নরেশের কাছে জানতে চাওয়া হল বিহারে যাবতীয় আত্মীয়স্বজনের নাম-ঠিকানা ইত্যাদি। জেনে নেওয়া হল, কোথায় কোথায় আশ্রয় নিতে পারেন পালিয়ে।
তিনটে টিম করা হল। যাঁরা ১৭ তারিখ দুপুরেই বেরিয়ে পড়লেন বিহারে। সম্ভাব্য সমস্ত আস্তানায় রেইড করা হল দিনের পর দিন। আজ সমস্তিপুর, কাল গয়া, পরশু জামুই, তরশু ঘাটশিলা। আত্মীয়বন্ধুদের বাড়িতে এক-দু’-দিন করে থাকছিলেন বীরেশ। পুলিশ পৌঁছনোর আগেই ডেরা বদলে ফেলছিলেন। প্রায় দশ-বারো দিন ধরে বিহারের পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ চষে ফেলেও নাগাল পাওয়া গেল না বীরেশের। ফিরে এলেন হতোদ্যম অফিসাররা।
বীরেশের মোবাইল না থাকলেও দাদা নরেশের ছিল। যে ফোনের উপর নজরদারি চালু হয়ে গিয়েছিল ঘটনার পরের দিন বিকেল থেকেই। অফিসাররা যেদিন ফিরে এলেন বিহার থেকে, তার পরের দিনই ফোন-নজরদারিতে ইঙ্গিত মিলল, টাকা ফুরিয়ে গেছে বীরেশের। দু’-এক দিনের মধ্যেই কলকাতায় আসার সম্ভাবনা। দেখা করতে পারেন দাদার সঙ্গে। জাল পাতা হল শহরের স্টেশনে-বাস টার্মিনাসে-ফেরিঘাটে। ৩১ ডিসেম্বর বর্ষশেষের সন্ধেয় বাবুঘাটে গোয়েন্দাদের হাতে ধরা পড়লেন স্ত্রী এবং পাঁচ কন্যাকে খুন করে ফেরার হয়ে যাওয়া বীরেশ।
জেরাপর্বে বীরেশ কোনও রাখঢাকের রাস্তায় গেলেন না। কয়েক লাইনে লিখে গিয়েছিলেন যে স্বীকারোক্তি, সেটাই বললেন বিস্তারে। যখনই রীতাকে কোনও কারণে কথা বলতে দেখতেন দিগ্বিজয়ের সঙ্গে, তীব্র অশান্তি হত সংসারে। ছোটখাটো ঘটনা নিয়েও স্বামী-স্ত্রীর খিটিমিটি লেগেই থাকত। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অবধারিত ভাবে বীরেশ টেনে আনতেন দিগ্বিজয়ের সঙ্গে সম্পর্ককে। ঘটনার মাসখানেক আগে যেমন। সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে বীরেশ দেখলেন, একটা মাঝারি মাপের সুটকেস এক কোণে রাখা।
—রীতা, এটা কার? কোত্থেকে এল?
—দিগ্বিজয় ভাইয়ার। ওর ঘরে কিছু মেরামতির কাজ চলছে। জায়গার অভাব। তাই বিকেলে ভাইয়া এসে বলল, দু’-তিন দিনের জন্য যদি এটা..
—ভাইয়া! ভাইয়া, না সাঁইয়া? সব জানা আছে আমার, এ সুটকেস এখানে থাকবে না। রাস্তায় রাখুক সুটকেস, আমার বাড়ি ছাড়া আর জায়গা পেল না?
সঙ্গে সঙ্গেই উলটোদিকের ঘরে গিয়ে সুটকেস রেখে এসেছিলেন বীরেশ, তপ্ত বাদানুবাদ হয়েছিল স্বামী-স্ত্রীর।
মনে সন্দেহের বীজ দাম্পত্য জীবনের শুরু থেকেই লালন করে এসেছিলেন বীরেশ। বিয়ের তিন মাসের মধ্যেই গর্ভবতী হন রীতা এবং বীরেশের ধারণা হয়, এ সন্তান তাঁর ঔরসজাত নয়। ভুল ভাঙানোর আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন রীতা।
এরপর একে একে আরও চার কন্যাসন্তানের জন্ম। তাদের একটু একটু করে বড় হয়ে ওঠা। যত বছর গড়িয়েছে, সন্দেহের তীব্রতা প্রশমিত হওয়া দূরে থাক, কোনও কার্যকারণ ছাড়াই বীরেশের ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে, সন্তানরা তাঁর নয়। রীতার অবৈধ সম্পর্কের ফসল। এই ধারণায় ঘৃতাহুতি দিয়েছিল গত কয়েক বছরে রীতা-দিগ্বিজয়ের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠা। দিগ্বিজয় ডাকতেন ‘রীতা ভাবি’ বলে। রীতা ডাকতেন ‘ভাইয়া’। বীরেশ মনে করতেন, ওসব লোকদেখানো। আসলে অন্য সম্পর্ক আছে।
—আমি বারবার ওকে বারণ করতাম দিগ্বিজয়ের সঙ্গে কথা বলতে। রীতা শুনত না। তর্ক করত। বলত, ‘বিনা কারণে কথা বন্ধ করব কেন?’ শুনে খুন চেপে যেত মাথায়।
প্রতি সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে মেয়েদের কাউকে না কাউকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করতেন বীরেশ, ‘আজ দিগ্গিচাচা ঘরে এসেছিল? মা ওঘরে গিয়েছিল? গল্প করতে দেখেছিস?’
সন্দেহ ক্রমে জিঘাংসায় পরিণত হওয়া যদি খুনের প্রথম কারণ হয়, দ্বিতীয় ছিল উপর্যুপরি পাঁচ কন্যাসন্তানের জন্ম। দুর্ভাগা দেশ আমাদের, ছেলে কেন হচ্ছে না, সন্তান প্রসবের পর প্রতিবারই এ নিয়ে বীরেশ কাঠগড়ায় তুলতেন রীতাকে। চতুর্থবার যখন যমজ কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হল, বীরেশের ধৈর্য বিদ্রোহ করল।
—স্যার, ঘুম আসত না রাতের পর রাত। সামান্য ব্যবসা করি, কীভাবে বিয়ে দেব
পাঁচ-পাঁচটা মেয়ের? আর রাগ হত রীতার উপর। পাঁচটাই মেয়ে, একটা ছেলে হতে পারত না?
পালটা কী-ই বা বলা যেত প্রস্তরযুগীয় মানসিকতায় আচ্ছন্ন এই অল্পশিক্ষিত যুবককে? পৃথ্বীরাজ পরের প্রশ্নে গিয়েছিলেন।
—স্ত্রীকে মারলেন কেন, বুঝলাম। কিন্তু নিজের বাচ্চা মেয়েগুলোকে ওভাবে …
কথা শেষ করতে দেন না বীরেশ।
—আমি আর পারছিলাম না বউ আর পাঁচ-পাঁচটা মেয়ের বোঝা টানতে। আর, নিজের বাচ্চা কে বলল স্যার? নিজের কিনা সেটা নিয়েই ধন্দে থাকতাম সবসময়।
পৃথ্বীরাজ বোঝেন, এই লোকের সঙ্গে তর্ক বৃথা। কথায় কথাই বাড়বে শুধু। তার চেয়ে বরং জিজ্ঞেস করা যাক সে-রাতের ঘটনাক্রম।
—আমি ঠিক করে ফেলেছিলাম স্যার, বউ-বাচ্চাদের তো মারবই, দিগ্বিজয়কেও বাঁচতে দেব না। কাঠের কাজ করি। নানা ধরনের ছুরি ব্যবহার করতে হয়। একটা ধারালো ছুরি বাড়িতে এনেছিলাম সেদিন। আর কিনে এনেছিলাম একপাতা ঘুমের বড়ি।
—কী বড়ি?
—ভ্যালিয়াম-৫ স্যার। ঘুমের ওষুধ তো প্রেসক্রিপশন ছাড়া ডাক্তাররা দিতে চাইবে না, জানতাম। এক বন্ধুর কাকা ডাক্তার ছিলেন। উলটোডাঙার কাছে চেম্বার। বন্ধুকে ধরলাম। ওর সঙ্গে গেলাম ডাক্তারবাবুর কাছে। বললাম, গত দু’সপ্তাহ ধরে রাতে ঘুম হচ্ছে না। অস্থির লাগছে সারাদিন। একটা উপায় করুন রাতে ঘুমোনোর। ডাক্তারবাবু প্রেশার দেখলেন। ঘুমের ওষুধ দিতে চাইছিলেন না। আমি খুব কাকুতিমিনতি করায় রাজি হলেন। ওষুধ কিনে বাড়ি ফিরলাম।
—তারপর?
—আমরা সকলেই রাতে দুধ খেয়ে শুতাম। রীতা যখন বাচ্চাদের জন্য বিছানা করছে, আমি ওর গ্লাসে দুটো ঘুমের বড়ি ফেলে দিলাম। বাচ্চাদের হাতে এক একটা করে বড়ি দিয়ে বললাম, এগুলো ভিটামিন ট্যাবলেট। ওরা চুপচাপ খেয়ে নিল। আমরা সাড়ে দশটা-পৌনে এগারোটা নাগাদ শুয়ে পড়লাম। আমি আর রীতা মেঝেতে শুতাম। মেয়েরা খাটে। আমি জেগে থাকলাম, কখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে, তার অপেক্ষায়।
—বলতে থাকুন।
বীরেশ বলতে থাকলেন নির্বিকার। বর্ণনা থাকুক তাঁরই বয়ানে, একটানা।
—ওরা সবাই ঘুমিয়ে পড়ল কিছুক্ষণ পরেই। আমি উঠলাম। সব ঠিক করে রেখেছিলাম আগে থেকেই। প্রথমে রীতাকে মারলাম। উলের চাদর ছিল একটা ওর। আলনায় রাখা ছিল। সেটা দিয়ে ফাঁস দিলাম গলায়। নাকের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে দেখলাম, নিশ্বাস পড়ছে না।
খাটে উঠলাম এবার। আমাদের খাটটা ঘরের ডানদিকের দেওয়ালে লাগানো ছিল। একদম বাঁদিকে রিমা শুত। বড়মেয়ে। ওকে মারলাম ওরই ওড়নার ফাঁস দিয়ে।
তারপর প্রীতি, মেজো। কয়েকদিন হল একটু ঠান্ডা লেগেছিল ওর। গলায় মাফলার ছিল। ওটাই চেপে ধরলাম গলায়।
প্রীতির পাশে ছিল স্মৃতি। পাশ ফিরে শুয়েছিল। ঘুমে কাদা, সোজা করে দিলাম। আলনায় রাখা মাফলার দিয়ে গলাটা চেপে ধরলাম।
দেওয়ালের দিকে পাশাপাশি শুত শ্বেতা আর ভাবনা। যমজ ওরা। বড়মেয়ে রিমার ওড়নাগুলোর কয়েকটা রাখা থাকত আলনায়, কয়েকটা ঝুলত দরজার হুকে। দুটো ওড়না নিলাম। তাই দিয়ে প্রথমে শ্বেতা। তারপর ভাবনা। তারপর ছুরিটা নিয়ে দিগ্বিজয়ের ঘরে নক করলাম।…
এবার বীরেশকে থামিয়ে দেন পৃথ্বীরাজ। স্ত্রী-সন্তানদের হত্যার এই নিস্পৃহ ধারাবিবরণী একটানা শোনা দুঃসাধ্য হয়ে উঠছিল। কেস ডায়েরি লেখার প্রয়োজনে প্রায়ই দেখতে হয় বাচ্চাগুলোর মৃতদেহের ছবি। যতবার দেখেন, কান্না জমে গলার কাছে। আর এ বাবা হয়ে কী অনায়াসে বলে যাচ্ছে!
কেসের কিনারা হয়ে গেছে। অপরাধী ধরা পড়ে গেছে। তবু যে প্রশ্নের উত্তর না পেলেই নয়, সেটা করেই ফেলেন পৃথ্বীরাজ। পারা যাচ্ছিল না আর।
—সন্দেহ করতেন স্ত্রীকে, বুঝলাম। কিন্তু বাচ্চাগুলো তো কোনও দোষ করেনি। ওদের এভাবে মেরে ফেললেন ঘুমের মধ্যে? একটুও কষ্ট হল না? আর মারলেনই যদি, স্বীকারোক্তি লিখে গেলেন কেন? আজ নয় কাল, আমরা তো ধরতামই আপনাকে।
আবেগের ন্যূনতম বহিঃপ্রকাশ ছিল না বীরেশের উত্তরে।
—স্বীকারোক্তিটা ঝোঁকের মাথায় লিখেছি। ওটা উচিত হয়নি। আর মেয়েগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেই বা কী লাভ হত স্যার? আমি তো ভেবেছিলাম, বিহারে পাকাপাকিভাবে পালিয়ে যাব। ব্যবসা করব কিছু। কী লাভ হত ওদের বাঁচিয়ে রেখে? কে দেখত ওদের? দাদার নিজের সংসার ছিল, সম্ভব হত না পাঁচটা মেয়ের ভার নেওয়া। বেঁচে থাকলে ওদের অসুবিধেই হত। উপায় ছিল না এ ছাড়া। তা ছাড়া ওই যে বললাম, আমারই যে মেয়ে সেটাই তো…
আর সহ্য করতে পারেন না পৃথ্বীরাজ, ফের থামিয়ে দেন বীরেশকে। বোঝেন, এই লোক বাহ্যত সুস্থ, আসলে গভীর মনোবিকারগ্রস্ত। পরকীয়াজনিত সন্দেহে স্বামী খুন করেছে স্ত্রীকে, এমন ঘটনা অনেকই ঘটে। কিন্তু স্ত্রী এবং পাঁচটা নিষ্পাপ মেয়েকে এভাবে প্ল্যান করে মারার পরও কীভাবে কেউ সেই নিধনবৃত্তান্ত শোনাতে পারে নির্বিকার? কথাবার্তায় না আছে লেশমাত্র অনুতাপ, না আছে শোকের সামান্যতম চিহ্ন।
চার্জশিট পেশ করলেন পৃথ্বীরাজ। দিগ্বিজয়কে ছুরি মারার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন দু’জন। দিগ্বিজয় স্বয়ং, আর তাঁর ছেলে কৌশল। দিগ্বিজয় ভয়ংকর জখম হয়েও প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন দ্রুত চিকিৎসা শুরু হওয়ায়। বীরেশের পালানোর সাক্ষী ছিলেন দুই প্রতিবেশী, সত্যদেও আর রামচল। বীরেশের হাতের লেখার নমুনার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল স্বীকারোক্তির চিরকুটের হস্তাক্ষর। প্যাসেজে পড়ে থাকা রক্তমাখা ছুরিতে পাওয়া গিয়েছিল বীরেশের আঙুলের ছাপ। বাড়ির পিছনের উঠোন থেকে উদ্ধার হয়েছিল ভ্যালিয়াম ৫-এর খালি স্ট্রিপ। যে ওষুধের দোকান থেকে বীরেশ কিনেছিলেন ওষুধ, সেই ‘Popular Drug House’-এর দোকানদার চিহ্নিত করেছিলেন অভিযুক্তকে।
জাল কেটে বেরনোর রাস্তা ছিল না। বীরেশ তবু আদালতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছিলেন পুলিশকে দেওয়া বয়ান। জোরগলায় দাবি করেছিলেন আগাগোড়া, ‘আমি নির্দোষ।’ সমস্ত প্রমাণ বিপক্ষে, তবু একচুলও নড়েননি সে দাবি থেকে।
বিচারসিদ্ধান্তের আনুগত্য থাকে শুধু প্রমাণের প্রতি। অভিযুক্তের সারবত্তাহীন দাবির প্রতি নয়। ধোপে টেকেনি বীরেশের দাবি, দায়রা আদালত দীর্ঘ বিচারপর্বের পর ২০০৬ সালে বীরেশকে দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন। যাবজ্জীবন কারাবাস, না ফাঁসি, জল্পনা তুঙ্গে উঠেছিল সেসময়।
বিচারক সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন বীরেশকে, ‘যা অপরাধ করেছেন, কী সাজা হওয়া উচিত বলে মনে হয় আপনার?’ বীরেশ বলেছিলেন ‘আমার বয়স এখন ৪৬। আমার কোনওরকম অপরাধের কোনও অতীত রেকর্ড নেই। আপনি যদি মনে করেন ফাঁসি দেবেন, দিন। আমি বারবার বলে এসেছি, আমি নির্দোষ। এখনও তাই বলছি।’
ফাঁসি হয়নি। সাজা হয়েছিল যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের। হাইকোর্টে সাজা রদের আবেদন করেছিলেন বীরেশ। লাভ হয়নি। শাস্তি বহাল থেকেছিল।
অপরাধ-মনস্তত্ত্ব নিয়ে বিশ্বজুড়ে কত যে গবেষণা হয়ে এসেছে কয়েক শতক ধরে, কত যে নতুন চিন্তাপ্রবাহ প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ করে চলেছে অপরাধবিজ্ঞানকে, হিসেব রাখা কঠিন। আমার-আপনার থেকে কোথায় কতটা আলাদা ভয়ংকর অপরাধীদের মস্তিষ্কের গঠন, ব্রেনের আকৃতির তারতম্য কীভাবে আলাদা করে দেয় সামান্য ছিঁচকে চোরের সঙ্গে সিরিয়াল কিলারের মনোজগতের, সে নিয়ে বিদগ্ধ অধ্যয়ন জারি রয়েছে দেশে-বিদেশে।
তবে কিনা, বিষয়টা তো দিনের শেষে মন। কে আর কবে মনের পাসওয়ার্ড সম্পূর্ণ ভেদ করতে পেরেছে গবেষণায়-আলোচনায়-পরীক্ষানিরীক্ষায়? আর এ তো বিরল অপরাধীর মন, যেখানে সন্দেহের বীজ সযত্ন পরিচর্যায় ক্রমশ আক্রোশের মহীরুহে পরিণত হয়। এবং ঘটে যায় এমন অপরাধ, যা লজ্জায় ফেলবে সুদূরতম কল্পনাকেও। কী উপাদানে তৈরি হয় বীরেশ পোদ্দারদের মনোজগৎ? যা প্ররোচিত করে ঠান্ডা মাথার পরিকল্পনায় অচিন্তনীয় অপরাধে, বাধ্য করে অপরাধের স্বীকারোক্তি-লিখনে, এবং আইনের কাছে পরাভূত হওয়ার প্রাক্কালে সেই স্বীকারোক্তিকেই নির্দ্বিধায় খণ্ডনে?
এই লেখা লিখতে গিয়ে মনে হয়েছে বারবার, হয়তো পড়তে পড়তে আপনাদেরও, কিছু অপরাধ তোয়াক্কা করে না ব্যাখ্যার। কিছু অপরাধী হেলায় অগ্রাহ্য করে বিশ্লেষণকে, স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিকে।
সে আপনি যতই গভীরে যান। এই বুঝি তল পাবেন, ফের হারাবেন।
২.০৬ ফেলুদাং শরণং গচ্ছামি
[ললিতা গোয়েঙ্কা হত্যা
আশিক আমেদ, ওসি, মেটিয়াবুরুজ।]
— মা-কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না… তুমি শিগগির বাড়ি এসো…
অনিল গোয়েঙ্কার মোবাইলটা যখন বেজে উঠল, সকাল তখন কত? এই পৌনে আটটা। ব্যাট-প্যাড পরে মাঠে নামতে যখন রোদের দেরি থাকে কিছু। আবার ভোরের আধো-অন্ধকারও যখন প্যাভিলিয়নের পথে। মাঝামাঝি একটা সময়। ভোর আর সকালের প্রাত্যহিক চুক্তিতে যখন সব ‘শান্তিকল্যাণ’ হয়ে আছে।
মঙ্গল-বৃহস্পতি-রবি, সপ্তাহে তিনদিন টালিগঞ্জ ক্লাবে ভোরবেলা গল্ফ খেলতে আসা অনিলের বহুদিনের অভ্যেস। আজ, বিষ্যুদবারে, যেমন এসেছেন। দু’রাউন্ড খেলার পর সবে একটু জিরিয়ে নিচ্ছেন যখন, গলা ভিজিয়ে নিচ্ছেন ফ্রেশ ফ্রুট জুসে, স্ত্রী জয়শ্রীর ফোন। মা-কে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না! অনিলের উত্তরে ঠিকরে বেরয় অস্থিরতা-উদ্বেগ-আশঙ্কা।
—কী বলছ কী? খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না মানে? বাথরুমে দেখেছ?
—দেখেছি। নেই। বিছানায় রক্তের দাগ আছে। সব ওলটপালট। মেঝেতেও রক্ত আছে… আমার হাত-পা কাঁপছে… এসো শিগগির…
গল্ফ মাথায় উঠল। দ্রুত গাড়িতে উঠে বসলেন অনিল। ড্রাইভারের প্রতি সামান্য উত্তেজিত নির্দেশ এল।
—ঘর চলো… জলদি!
‘ঘর’, অর্থাৎ ‘শ্রীনিকেত অ্যাপার্টমেন্টস’। ১১, অশোকা রোড, আলিপুর।
অনিল যখন পড়িমরি করে বাড়ি পৌঁছে পা রাখলেন বাড়ির দরজায়, ভিড় জমে গেছে প্রতিবেশীদের। থমথমে মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন ছোটভাই সুনীল। দাদাকে দেখেই বললেন, ‘ভাইয়া… কুছ গড়বড় হ্যায়… পুলিশ কো বুলানা চাহিয়ে।’
‘গড়বড়’ যে আছেই, সেটা বুঝতে অবশ্য তেমন বুদ্ধি খরচের দরকার পড়ে না। ফ্ল্যাটে এক চক্কর দিলেই মালুম হয় অনায়াসে।
আসলে দুটো ফ্ল্যাট একসঙ্গে। এগারো তলায়, 10D আর 10E। আয়তনের বিচারে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে মাঝারি সাইজ়ের ফুটবল মাঠের সঙ্গে। সব মিলিয়ে আটটা ঘর। প্রতিটাই পেল্লায় সাইজ়ের। অপর্যাপ্ত বৈভবের চিহ্ন ছড়িয়ে ফ্ল্যাটের এ-মাথা থেকে ও-মাথা। বিরাট হলঘরে সেগুনকাঠের রকমারি আসবাবপত্র। দুর্মূল্য তৈলচিত্র। বাহারি সোফাসেট। সিলিং থেকে ঝুলতে থাকা কারুকাজের ঝাড়লন্ঠন। প্রশস্ত ড্রয়িংরুম পেরিয়ে আরও প্রশস্ত বারান্দা। যার পাশে বিস্তৃত খোলা জায়গা একটা, ‘ওপেন টেরেস’। যেখানে দাঁড়িয়ে চোখ তুলে চাইলে আকাশকে খুব দূরের মনে হয় না।
আটটার মধ্যে সাতটা ঘর যেমন থাকার তেমন। একটা শোওয়ার ঘরের চেহারা শুধু বিধ্বস্ত। বিছানা ওলটপালট। দুটো বালিশ ঝুলছে খাটের এক কোণে। বেডসাইড টেবিল থেকে একটা জলের গ্লাস উলটে পড়েছে মেঝেতে। প্রায় দু’ফুট লম্বা একটা জিআই পাইপ পড়ে আছে খাটের নীচে। বিছানার উপর অন্তত চারটে জায়গায় লাল ছোপছোপ। রক্ত, বোঝা যায় সাদা চোখেই।
যিনি এই বিছানায় শুতেন, শুয়েছিলেন গত রাতেও, সেই ললিতাদেবী গোয়েঙ্কা কোথায়? সত্তর বছরের বৃদ্ধা কোত্থাও নেই। অন্য ঘরগুলোয় নেই। রান্নাঘরে নেই। শোওয়ার ঘরের লাগোয়া বাথরুমে নেই। হলঘরের এক কোনায় আর একটা বাথরুম। যেটা কখনও ব্যবহার হয় না। খুলে দেখা হল। নেই।
ছাদে-বারান্দায়-টেরেসে-ঠাকুরঘরে? নেই। একটা জায়গাই দেখার পড়ে আছে। স্টোররুম। তালা ঝুলছে দরজায়। যেমন ঝোলে রোজ। শোওয়ার ঘরের ড্রেসিং টেবলের ড্রয়ারে চাবি থাকে। ‘থাকে’ নয়, থাকত। দ্রুত আবিষ্কৃত হল, স্টোররুমের চাবি ড্রয়ারে নেই।
অনিল গোয়েঙ্কার মুখ রক্তশূন্য হয়ে যায় এবার। চাবিটা কোথায় গেল স্টোররুমের? মা কোথায়? তা হলে কি…? মোবাইলে আলিপুর থানার নম্বর যখন ডায়াল করছেন, হাত কাঁপতে শুরু করেছে।
—একবার আপনাদের আসতে হবে বড়বাবু। মা-কে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। স্টোররুমের চাবি মিসিং। বেডরুমটা ডিস্টার্বড। ব্লাড স্টেইনস আছে বেডে। একবার যদি আসেন এখনই… প্লিজ়…
পুলিশ পৌঁছল, স্টোররুমের তালা ভাঙা হল এবং ভিতরের দৃশ্য দেখে মুহূর্তে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন ললিতা গোয়েঙ্কার পুত্রবধূ জয়শ্রী। অনিল দাঁড়িয়ে রইলেন স্তব্ধ হয়ে। মুখে হাত ঢেকে ডুকরে কেঁদে উঠলেন সুনীল।
মেঝে রক্তে থইথই। বৃদ্ধা পড়ে আছেন নিষ্প্রাণ। মুখে কাপড় গোঁজা। কপালে গভীর ক্ষতচিহ্ন। গলার নলিটা কাটা। যা দিয়ে কাটা হয়েছে সম্ভবত, সেই ছুরিটা পড়ে আছে পেটের উপর। যে ফুল-ফুল খয়েরি-সাদা ম্যাক্সিটা মহিলার শরীরে, সেটার রং প্রায় পুরো বদলে গিয়ে লালে লাল। রক্তপাত হয়েছে প্রচুর। দুটো সাদা বেডশিট পড়ে আছে দুমড়ানো-মুচড়ানো। রক্তের দাগ যাতে যত্রতত্র।
স্টোররুমে দুটো বড় আলমারি। দুটোই লন্ডভন্ড। হাতড়ানো হয়েছে বেপরোয়া। কী থাকত আলমারিগুলোয়? অনিল জানালেন, মায়ের জমানো টাকাপয়সা থাকত ছোট ছোট কাপড়ের পুঁটলিতে। যার একটাও আলমারিতে নেই এখন। মৃতদেহের পাশে একটা একশো টাকার নোটের বান্ডিল পড়ে আছে হেলাফেলায়। যে বা যারা খুনটা করল, পালানোর সময় তাড়াহুড়োয় নিতে ভুলে গেছে?
প্রায় সাত হাজার বর্গফুটের ফ্ল্যাটের প্রতিটি ইঞ্চি-সেন্টিমিটারের তন্নতন্ন তল্লাশিতে ঘণ্টা দুয়েক লেগে গেল আলিপুর থানার পুলিশের। যাদের সঙ্গে যোগ দিলেন গোয়েন্দাবিভাগের হোমিসাইড শাখার অফিসাররা। দ্রুত চলে এলেন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা। খোঁজাখুঁজিতে উল্লেখ করার মতো জিনিস বলতে পাওয়া গেল দুটো কালো রংয়ের প্লাস্টিকের বোতাম। পড়ে ছিল খাটের নীচে এক কোনায়। খুনি বা খুনিদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি হয়েছিল মহিলার? সাধ্যমতো প্রতিরোধ করেছিলেন, এবং আততায়ী বা আততায়ীদের কারও শার্ট থেকে বোতাম দুটো ছিঁড়ে গিয়েছিল টানাটানিতে?
জিআই পাইপটা খাটের নীচে এল কোথা থেকে? বারান্দার একধারে চারটে পাইপ পড়েছিল বেশ কিছুদিন যাবৎ। তারই একটা নিয়ে জোরালো আঘাত করা হয়েছিল মৃতার কপালে।
‘Seizure list’-এর তালিকায় ওই লোহার পাইপের সঙ্গে যোগ হল রক্তের দাগ লাগা বালিশ, স্টোররুমে পড়ে থাকা রক্তমাখা এক জোড়া বেডশিট, মৃতার পেটের উপর পড়ে থাকা ছুরি, একশো টাকার নোটের বান্ডিল। আলমারিতে আঙুলের ছাপ? বা খাট-বিছানায়? পাওয়া গেল আবছা, ‘ডেভেলপ’ করার যোগ্য নয়।
অভিজাত আবাসনে সম্পন্ন ব্যবসায়ী পরিবারে সত্তর বছরের বৃদ্ধার নৃশংস খুন। গলাকাটা অবস্থায় দেহ উদ্ধার ফ্ল্যাটের স্টোররুম থেকে। মিডিয়ায় হইচই হবে, স্বাভাবিকই ছিল। যেমন স্বাভাবিক ছিল দেহ উদ্ধারের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তদন্তভার নেওয়া হোমিসাইড বিভাগের। সাব-ইনস্পেকটর আশিক আমেদ (বর্তমানে মেটিয়াবুরুজ থানার ওসি) দায়িত্ব পেলেন রহস্যভেদের।
ললিতাদেবী গোয়েঙ্কা হত্যারহস্য। আলিপুর থানা, কেস নম্বর ১১৭, তারিখ ১২/৮/২০০৪। খুন, লুঠ এবং প্রমাণ লোপাট। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩৯৪/২০১ ধারায়।
.
শ্রীনিকেত অ্যাপার্টমেন্টস। ছিমছাম কোলাহলহীন রাস্তার উপর ভিতরে-বাইরে গাছগাছালির সবুজ আবাসন। দুটো আলাদা ব্লক। ‘এ’ আর ‘বি’। দুটোই এগারো তলা। ব্লক এ-র দশ আর এগারো তলায় দুটো করে ফ্ল্যাট। বাকি প্রতিটা ফ্লোরে চারটে করে ফ্ল্যাট। একতলায় পার্কিং স্পেস রয়েছে পর্যাপ্ত, যেমন থাকে এ ধরনের আবাসনে।
নিরাপত্তায় যথেষ্ট বিনিয়োগ করেছিলেন আবাসিকরা। প্রায় পনেরো ফুটের কাছাকাছি উচ্চতার পাঁচিল। যার উপর তার দেওয়া, ‘barbed wire fencing’।
ঢোকার-বেরনোর একটাই গেট। যেটা পেরিয়ে ঢুকলেই পশ্চিম দিকে ‘security box’। বেসরকারি সংস্থা ‘Royal Securities Pvt Ltd.’-র কর্মীরা থাকেন নিরাপত্তার দায়িত্বে। ব্লক এ-র একতলায় আবাসনের অফিস, ‘শ্রীনিকেত হাউসিং এস্টেট সোসাইটি’।
সিকিউরিটি বক্সে ইন্টারকম আছে। বাইরে থেকে কেউ এসে কোনও ফ্ল্যাটে যেতে চাইলে নিরাপত্তাকর্মী ফোন করে ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের জানিয়ে দেয়, তমুক এসেছেন। সবুজ সংকেত পেলে তবেই প্রবেশাধিকার মেলে বহিরাগত অতিথির। ভিজিটর্স রেজিস্টারে নাম-ঠিকানা লিখে সই করার পর। রোজকার আংশিক সময়ের গৃহকর্মীদের, যাদের মুখ চেনা, ঢোকার ব্যাপারে বাধা নেই।
যাঁরা বিভিন্ন ফ্ল্যাটে স্থায়ী কাজের লোক, তাঁরা যখন ছুটিতে যান, ‘গেট পাস’ নিয়ে বেরতে হয়। বেরনোর সময় সঙ্গে যা যা থাকে ব্যাগ বা সুটকেসে, দেখাতে হয় নিরাপত্তাকর্মীদের। তারপর ছাড়পত্র মেলে বাইরে যাওয়ার। কে কখন বেরল আর ফিরল কবে কখন, সব নোট করা থাকে রেজিস্টারে।
প্রতি ব্লকে দুটো করে লিফট। দু’জন করে লিফটম্যান ব্লকপিছু। যাঁরা দুটো শিফটে কাজ করেন। সকাল ছ’টা থেকে দুপুর দুটো। দুপুর দুটো থেকে রাত দশটা। চারজন স্থায়ী সাফাইকর্মী রয়েছেন। রয়েছেন একজন ইলেকট্রিশিয়ান এবং একজন প্লাম্বার। হাউসিং-এর অফিসে আছেন একজন কেয়ারটেকার আর তাঁর একজন সহযোগী।
নিরাপত্তারক্ষীরা শিফটে কাজ করেন রাতদিন সাতদিন। দু’জন করে থাকেন সকাল ন’টা থেকে রাত ন’টা। পরের শিফট রাত থেকে সকাল, বারো ঘণ্টা টানা। দিনের শিফটে একজন সুপারভাইজ়ারও থাকেন।
এই আবাসন তৈরি করেছিলেন ভগবতীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা। ব্লক এ-তে দশ আর এগারো তলাটা নিজের পরিবারের জন্য রেখে বাকি ফ্ল্যাটগুলো বেচে দিয়েছিলেন। এগারো তলায় থাকতেন সস্ত্রীক। দশতলার দুটো ফ্ল্যাট লিখে দিয়েছিলেন দুই ছেলের নামে। বড় অনিল, ছোট সুনীল। আগেই লিখেছি, ব্লক দুটোর বাকি ফ্লোরগুলোর প্রতিটায় ছিল চারটে করে ফ্ল্যাট। গোয়েঙ্কাদের বাদ দিলে মোট ফ্ল্যাটের সংখ্যা আশি।
পি. ও। প্লেস অফ অকারেন্স। ঘটনা যেখানে ঘটেছে। যে-কোনও তদন্তে ঘটনাস্থল তদন্তকারীর কাছে মন্দির-মসজিদ-চার্চের মতো। তীর্থস্থানস্বরূপ। সাধকের ধৈর্য নিয়ে দেখতে হয়। পূর্ণাঙ্গ খানাতল্লাশির পর ফ্ল্যাটটা ভাল করে ঘুরে দেখছিলেন আশিক।
এগারো তলার যে ফ্ল্যাটে ললিতাদেবী থাকতেন, বলেছি আগে, তার নম্বর 10D & 10E। পাশাপাশি দুটো ফ্ল্যাটের পুরোটা নিয়েই বসবাস করতেন মহিলা। দুটো ফ্ল্যাট মিলিয়ে আটটা বড় ঘর, দুটো বড় হল, ডাইনিং রুম, একটা রান্নাঘর। প্রশস্ত বারান্দা যেখানে শুরু হচ্ছে, তার পাশেই বড় স্টোররুম। যেখানে আবিষ্কৃত হয়েছিল বৃদ্ধার দেহ।
দশতলায় দুটো ফ্ল্যাট। 9E এবং 9F। অনিল থাকেন 9E-তে। সুনীল 9F-এ।
অনিলের ফ্ল্যাটের ভিতর থেকে এগারো তলায় মায়ের ফ্ল্যাটে উঠে যাওয়ার একটা সিঁড়ি আছে। অনিল সপরিবারে উপরে মায়ের সঙ্গেই খাওয়াদাওয়া করতেন। রান্নাবান্নার সরঞ্জাম এগারো তলাতেই থাকত।
ছাদে ‘সার্ভেন্টস কোয়ার্টার’। যে ছাদের মালিকানা সম্পূর্ণত ছিল গোয়েঙ্কাদের। বাড়ির কাজের লোকদের জন্য ছাদ থেকে নেমে এগারো তলার রান্নাঘরে ঢোকার একটা দরজা ছিল। সেই দরজা খোলা থাকত দিনভর। রান্নাঘরের ওই দরজা দিয়েই ফ্ল্যাটে ঢুকত স্থায়ী কাজের লোকেরা। রাতের খাওয়ার পাট সাধারণত সাড়ে ন’টার মধ্যে চুকে যেত গোয়েঙ্কা পরিবারের। তারপর জয়শ্রী রান্নাঘরের দরজায় ভিতর থেকে ছিটকিনি দিয়ে দিতেন।
ললিতার নিত্যনৈমিত্তিক রুটিন? ভোর পাঁচটা থেকে সাড়ে পাঁচটার মধ্যে উঠে ঠাকুরঘরে চলে যেতেন। তার আগে দরজা খুলে দিতেন রান্নাঘরের। গৃহকর্মীরা নির্দিষ্ট সময়মতো এসে দশ এবং এগারো তলার কাজ শুরু করত। দুপুর দুটো থেকে বিকেল পাঁচটা অবধি ছিল কাজের লোকদের বিশ্রামের সময়।
ললিতার দেহ উদ্ধার হল ১২ অগস্ট সকালে। তার আগের রাতে মহিলা কিছু খাননি। একাদশী ছিল। রাত ন’টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। উপরের ফ্ল্যাটে রোজকার মতো সকাল সাড়ে সাতটা-পৌনে আটটা নাগাদ উঠে এসেছিলেন জয়শ্রী। জলখাবারের তদারকি করতে। এসে দেখেছিলেন, শাশুড়ি ফ্ল্যাটে নেই। ওলটপালট বিছানায় রক্তের দাগ। তারপর আতঙ্কিত ফোন অনিলকে, ‘মা-কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শিগগির বাড়ি এসো।’
.
ময়নাতদন্ত হতে হতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল। প্রত্যাশিত রিপোর্ট, গলায় ছুরির আঘাত এবং মাথায় গভীর ক্ষত থেকে অবিরাম রক্তক্ষরণ মৃত্যু ঘটিয়েছে, ante-mortem and homicidal। ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা মৃতদেহ দেখে যা অনুমান করেছিলেন, পোস্টমর্টেম রিপোর্ট সহমত হল তাতে। খুনটা ঘটেছে রাত তিনটে থেকে চারটের মধ্যে। ললিতা ভারী চেহারার ছিলেন, খুনি একাধিক হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।
‘একাধিক’ যে হতেই পারে, বোঝাই যাচ্ছিল। দেহ বেডশিটে মুড়ে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল স্টোররুমে। একের পক্ষে অসম্ভব নয়। কিন্তু কঠিন। ‘এক’ না ‘একাধিক’, ভাবার আগে প্রাথমিক তথ্যসংগ্রহের প্রয়োজন। রাত দশটা অবধি আবাসনে কাটালেন আশিক। যা যা জানলেন, যা যা শুনলেন, যা যা বুঝলেন জিজ্ঞাসাবাদে এবং কানাঘুষোয়, বাড়ি ফেরার পথে সাজিয়ে নিচ্ছিলেন মাথায়।
ললিতাদেবীর দুই ছেলের পারস্পরিক সম্পর্ক ভ্রাতৃসুলভ ছিল না। না থাকার কারণ? ভগবতীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা বড়ছেলেকে বেশি দায়িত্ববান মনে করতেন বলেই সম্ভবত যাবতীয় সম্পত্তি ‘প্রোবেট’ করে গিয়েছিলেন অনিলের নামে। অগাধ সম্পত্তির মালিকানা পেয়েছিলেন অনিল। ছোটছেলে সুনীলকে ব্যবসার যৎসামান্য অংশীদারিত্ব নিয়েই খুশি থাকতে হয়েছিল।
অর্থের সড়কপথেই অনর্থের প্রবেশ ঘটে থাকে সচরাচর। অনর্থ বলতে যা বোঝায়, এক্ষেত্রে তেমন কিছু হয়নি অবশ্য। তবে ভায়ে-ভায়ের সম্পর্কে যে ফাটল ধরেছিল, সেটা অজানা ছিল না কারও। পরলোকগত স্বামীর সিদ্ধান্তে ললিতার নীরব সমর্থন ছিল। বড়ছেলের সংসারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। অনিলের দুই স্কুলপড়ুয়া পুত্র-কন্যা ঠাকুমার অনিঃশেষ স্নেহের ভাগিদার হয়েছিল। উৎসব-অনুষ্ঠান ছাড়া দুই ভাইয়ের পরিবারের মধ্যে যোগাযোগ ছিল না বললেই চলে। সুনীল থাকতেন নিজের মতো, সপরিবার।
দশ এবং এগারো তলা মিলিয়ে সবসময়ের কাজের লোক আটজন। শিবু মাহাতো। রান্না করেন। এ বাড়িতে আছেন তা সাত-আট বছর হল। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনায়।
আশিস-অমলেশ। দুই ভাই। মূলত বাড়ির রোজকার বাজারহাটের দায়িত্বে। ওঁরাও বেশ কয়েক বছর ধরে আছেন গোয়েঙ্কা পরিবারে। হুগলিতে বাড়ি।
ত্রিলোকি সিং। বাড়ির সবচেয়ে পুরনো গৃহকর্মী। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে। আদতে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। নির্দিষ্ট কোনও দায়িত্ব নেই সেভাবে। বাকি গৃহকর্মীদের কাজের তদারকিই মূল কাজ। ব্যাংকের কাজ, চেক জমা দেওয়া, টাকা তুলে আনা, ইলেকট্রিক বিল জমা দেওয়া, এসবে ত্রিলোকির উপরই ভরসা করেন অনিল।
খগেন এবং রাজেশ। ললিতাদেবীর দেখাশুনোর দায়িত্ব ছিল এঁদের উপর। খগেনের বয়স বছর তিরিশ, বাড়ি ক্যানিং লাইনে। রাজেশের বয়স বাইশ-তেইশ। বাড়ি ওড়িশায়। দু’জনে প্রায় একসঙ্গেই কাজে ঢুকেছিলেন। বছর চারেক আগে।
সীতা এবং লক্ষ্মী। দুই মহিলা গৃহকর্মী। কাজের মধ্যে, ঘরদোর পরিষ্কার করা, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, টুকটাক ফাইফরমাশ খাটা ইত্যাদি। সীতার বয়স কুড়ির কোঠায়, বাড়ি হাওড়ায়। অবিবাহিতা। লক্ষ্মী মাঝবয়সি, বিবাহিতা। লক্ষ্মীকান্তপুরের বাসিন্দা। সীতা-লক্ষ্মী রাত্রে শুতেন দশতলায়, অনিলের ফ্ল্যাটের বারান্দার লাগোয়া একটা ঘরে।
ঘটনার রাতে, ১১/১২ অগস্ট, আটজন কাজের লোকের মধ্যে ছ’জন উপস্থিত ছিলেন। অমলেশের স্ত্রী-র একটি অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন ছিল। দেড় মাসের ছুটি নিয়েছিলেন। জুলাই মাসের ৮ তারিখ থেকে। ফের কাজে যোগ দেওয়ার কথা অগস্টের একুশ-বাইশ নাগাদ।
রাজেশের বাড়ি থেকে ফোন এসেছিল সপ্তাহখানেক আগে। বাবা অসুস্থ। এক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে বাড়ি গিয়েছিল ৮ অগস্ট। চলে আসার কথা পনেরো-ষোলো তারিখের মধ্যে।
অনিল-জয়শ্রী এবং কাজের লোকদের সঙ্গে দফায় দফায় প্রশ্নোত্তরে জানা গেল, ললিতাদেবীর সবচেয়ে বিশ্বাসভাজন ছিলেন তিনজন। কে কে?
লক্ষ্মী, দীর্ঘদিন আছেন বাড়িতে। যাঁকে খুবই ভালবাসতেন ললিতা। প্রতি পুজোয় হাজার খানেক টাকা বরাদ্দ রাখতেন। এটা-ওটা কিনে দিতেন প্রায়ই।
ত্রিলোকি, যাকে অনেক ছোট বয়স থেকে দেখেছিলেন ললিতা। পরিবারের সদস্যের মতোই স্নেহ করতেন। খোঁজখবর রাখতেন ত্রিলোকির বাড়ির লোকজনের। যে-কোনও আর্থিক সমস্যায় সাহায্য করতেন দরাজহস্ত।
রাজেশ, যাকে প্রায় পুত্রবৎ ভালবাসতেন বৃদ্ধা। মাঝেমাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়তেন ললিতা। তখন খাইয়ে দিত এই রাজেশই। বছরখানেক আগে উজ্জয়িনীতে তীর্থে গিয়েছিলেন ললিতা, সঙ্গে গিয়েছিল রাজেশই। অনিল জানালেন, ‘কাজের লোকদের মধ্যে শুধু ত্রিলোকি, লক্ষ্মী আর রাজেশের সঙ্গেই মা খোলামনে কথাবার্তা বলতেন।’
লক্ষ্মী এবং ত্রিলোকির সঙ্গে আলাদা করে অনেকক্ষণ কথা বললেন আশিক। আশাব্যঞ্জক কিছু পাওয়া গেল না। রইল বাকি রাজেশ। ফোন করে খবর পাঠানো হল ওড়িশার বাড়িতে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ফিরে আসতে বলা হল। ফিরে আসতে বলা হল অমলেশকেও, আরেকজন গৃহকর্মী, যিনি ছুটিতে ছিলেন।
‘সূত্র’ পাওয়ার লক্ষ্যে আবাসনের অন্যান্য স্থায়ী-অস্থায়ী কর্মীদেরও বিশদে জেরা করলেন আশিক। কাউকে বাদ দিলেন না। চার লিফটম্যান, লক্ষ্মণ-হিমাংশু-ইন্দ্রপাল-কৃষ্ণ। চার সুইপার, নিমাই-হিরামন-রামপ্রসাদ-লাল্টু। কেয়ারটেকার অচ্ছেবর সিং এবং তাঁর সহযোগী পল্টু ব্যানার্জি। জেরার ফল? বলার মতো কিছু? ভাবার মতো কিছু? না।
ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা করা হল গেটের নিরাপত্তারক্ষীদের। আদ্যন্ত খুঁটিয়ে দেখা হল ভিজিটর্স রেজিস্টার, পুরনো গেটপাস। রাত্রে তো নয়ই, কোনও বহিরাগত অতিথি ১১ অগস্টের পুরো দিনটাতেই ব্লক এ-র দশ তলা বা এগারো তলায় আসেননি। অন্যান্য ফ্ল্যাটগুলোর গৃহকর্মীদের আসা-যাওয়ার খতিয়ানেও কোনও অসংগতি নেই গেটপাসে, নেই সন্দেহ উদ্রেক করার মতো কিছু। রাতের শিফটের দুই নিরাপত্তাকর্মী সুনির্মল আর দীপক জোর গলায় দাবি করলেন, কেউ ঢোকেনি রাত্রে। প্রশ্নই নেই।
প্রশ্ন আছে কি নেই, ভাবতেই হত না সিসি টিভি থাকলে। এত সম্পন্ন একটা আবাসনে সিসি টিভি নেই, আশ্চর্য লাগে আশিকের। ‘শ্রীনিকেত অ্যাপার্টমেন্টস’ থেকে ১২ অগস্টের রাত্রে বেরনোর সময় ক্লান্ত আশিক ভাবতে থাকেন, কী কী কাজ বাকি আছে আর।
এক, প্রতিবেশীদের জিজ্ঞাসাবাদ। আজ সময়ই পাওয়া গেল না সেভাবে। গোয়েঙ্কা পরিবারের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে, বিশেষ করে অনিল-সুনীলের পারস্পরিক সমীকরণের বিষয়ে বিস্তারিত জানা দরকার।
দুই, প্রতিটি গৃহকর্মীর ‘ব্যাকগ্রাউন্ড চেক’ প্রয়োজন। প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে খোঁজখবর করা জরুরি। আবাসনের অন্য কর্মীদের ব্যাপারেও আরও খোঁজ নেওয়ার আছে।
তিন, যে দু’জন ছুটিতে ছিল, তারা কাল বা পরশু বিকেলের মধ্যে এসে পড়বে। বাড়তি তথ্য পাওয়া যেতেই পারে কিছু। যদি পাওয়া যায়, দেখতে হবে।
চার, ওই ফ্ল্যাটেরই শুধু নয়, আবাসনের কর্মীদের যাঁদের যাঁদের মোবাইল ফোন আছে তাঁদের কল রেকর্ডস আনাতে হবে। অন্তত গত সাতদিনের। এবং খুঁটিয়ে দেখতে হবে, দিশা পাওয়া যায় কিনা। আশিটা ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের ঠিকুজিকুষ্ঠি জানতে হবে। সবার মোবাইল নম্বর জোগাড় করে পাঠাতে হবে সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে। CDR (Call Details Records) নিতে হবে।
পাঁচ, কাল সকালেই একবার বসতে হবে ওসি হোমিসাইডের সঙ্গে। আলোচনা প্রয়োজন। ডিসি ডিডি তো নিজেই স্পটে এসেছিলেন, ছিলেন অনেকক্ষণ। ফোন করেছেন সন্ধে থেকে অন্তত তিনবার। সিপি-ও খোঁজ নিয়েছেন ওসি হোমিসাইডের কাছে। সবে তো প্রথম দিন। যত দিন যাবে, দ্রুত ‘ডিটেকশন’ করার চাপ উত্তরোত্তর বাড়বে, বুঝতে অসুবিধে হয় না আশিকের।
.
—অনেকগুলো খটকা স্যার… মেলানো মুশকিল…
আশিককে একটু চিন্তিত লাগে ওসি হোমিসাইডের।
—হুঁ… শুনছি, তার আগে বলো মোটিভটা কী মনে হচ্ছে?
—অ্যাপারেন্টলি তো মার্ডার ফর গেইন। স্টোররুমের আলমারি থেকে টাকাপয়সা নিয়ে গেছে।
—কত গেছে?
—এগজ়্যাক্ট অ্যামাউন্টটা বলা মুশকিল। অনিল প্রতি মাসে মা-কে কুড়ি হাজার হাতখরচা দিতেন। মহিলার মাসিক খরচ খুব বেশি ছিল না। নাতি-নাতনিকে এটা-ওটা কিনে দেওয়া, ঠাকুরঘরের টুকিটাকি জিনিস কেনা, বাড়ির কাজের লোকের মধ্যে ত্রিলোকি-রাজেশ-লক্ষ্মীর খুচরো সাধ-আহ্লাদ মেটানো। বাকিটা ছোট ছোট কাপড়ের পুঁটলিতে জমাতেন। অনিল বলছিলেন, লাখখানেক লাখ দেড়েকের মতো তো গেছেই।
—মিসলিড করার পসিবিলিটিটা মাথায় রেখেছ তো? কারণ হয়তো অন্য কিছু, তদন্তটা গুলিয়ে দেওয়ার জন্য লুঠপাট…
—হ্যাঁ, স্যার, সেটা তো মাথায় আছে… অন্য অঙ্ক থাকতেই পারে… আজ সকালেই এক পরিচিত অ্যাডভোকেটের ফোন এসেছিল… কাগজে খুনের খবরটা পড়ে কল করেছিলেন…
—কী বললেন?
—বললেন, পারিবারিক সম্পত্তির সিংহভাগ যে বড়ছেলের নামে ‘প্রোবেট’ করে গিয়েছেন ভগবতীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা, সেটা নিয়ে বিস্তর ক্ষোভ আছে ছোটছেলে সুনীলের…
—স্বাভাবিক…
—হ্যাঁ… সম্পত্তির ভাগ চেয়ে নাকি মামলা করার কথা ভাবছিলেন…
—বুঝলাম, কিন্তু ললিতাদেবীর মৃত্যুতে কি মামলায় কোনও সুবিধে হত সুনীলের?
—এমনিতে হওয়ার কথা নয়, তবু একটু কথা বলা দরকার ওই অ্যাডভোকেটের সঙ্গে… উনি আজ কলকাতার বাইরে আছেন… কাল সন্ধেবেলা যাব…
—হ্যাঁ… আর ওই খটকার কথা কী বলছিলে…
—রান্নাঘরের দরজাটা স্যার…
—মানে?
—বলছি স্যার। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে, খুনটা হয়েছে রাত তিনটে থেকে চারটের মধ্যে।
—তো?
—রোজ ভোর পাঁচটা-সাড়ে পাঁচটায় উঠে ললিতা রান্নাঘরের দরজা খুলে ঠাকুরঘরে যেতেন। মানে, ১২ অগস্টের ভোরে রান্নাঘরের দরজা খোলার স্কোপই ছিল না। তার আগেই মৃত্যু।
—হুঁ…
—অথচ জয়শ্রী সকালে সাড়ে সাতটা-আটটা নাগাদ উপরে গিয়ে দেখেছিলেন, রান্নাঘরের দরজা খোলা। ভিতর থেকে কেউ খুলে দিয়েছিল, এবং সেটা রাত তিনটের আগে। কে খুলল? কারা খুলল? যে বা যারা খুলল, তারা ভিতরে ঢুকল কী করে?
—বলে যাও…
—এটা পরিষ্কার, খুনি বা খুনিরা ওই রান্নাঘরের দরজা দিয়ে ঢুকেছিল। এ ছাড়া রাস্তা নেই ঘরে ঢোকার।
—যদি না মূল দরজায় কেউ বেল বাজায়, এবং মধ্যরাতে উঠে ললিতাদেবী দরজা খুলে দিয়ে থাকেন…
—সে সম্ভাবনা প্রায় শূন্য স্যার। ললিতা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন রোজকার মতো রাত সাড়ে ন’টায়। উপোস ছিল, খাননি। অনিল বলছেন, অচেনা লোক হলে রাতে দরজা খুলতেনই না। আর রাতে কেউ আসতও না।
—অচেনা লোক হলে খুলতেন না, কিন্তু যদি চেনা লোক হয়?
—চেনা লোক বলতে তো অনিলের পরিবার আর সুনীলের পরিবার…
—অনিলের পরিবারের কেউ হলে তা বাইরে থেকে ঢোকার দরকার পড়বে না, দশ থেকে এগারো তলায় ওঠার সিঁড়ি তো আছে ভিতর থেকেই।
—এগজ়্যাক্টলি মাই পয়েন্ট স্যার .. তা হলে পড়ে থাকছেন সুনীল…
—দেখতে গেলে তা-ই, কিন্তু কেন মারবেন মা-কে?
—মেরেছেন তো বলছি না… নিজের মা-কে ওইভাবে ছুরি দিয়ে… টাকাপয়সা নিয়ে… হাইলি আনলাইকলি…
—কিন্তু ধরো যদি উনি বেল বাজালেন, ললিতা ছোটছেলের আওয়াজ শুনে দরজা খুললেন, আর সুনীলের লাগানো ভাড়াটে গুন্ডারা, যারা অপেক্ষায় ছিল বাইরে, কাজটা করল…
—তাতেও ওই মোটিভের ব্যাপারটা অস্পষ্টই থাকছে।
—হুঁ!
—বাড়ির কাজের লোকদের কারও বা কয়েকজন মিলে খুনটা করার সম্ভাবনা সবথেকে বেশি। সবাই নিম্নবিত্ত পরিবারের। মোটিভ? টাকা।
—আরও ডিটেলে খোঁজ নাও সবার ব্যাপারে।
—নেব স্যার, প্রত্যেকের বাড়ির আর্থিক অবস্থা, শখ-আহ্লাদ-নেশা, সব আজ-কালের মধ্যে পেয়ে যাব আশা করছি। লোক লাগানো হয়ে গেছে।
—বেশ…
—স্যার, ওসব ইনফর্মেশন না হয় জোগাড় হয়েই যাবে, কিন্তু রান্নাঘরের দরজার খোলা থাকাটা কিছুতেই মেলাতে পারছি না। কে খুলল, কীভাবে খুলল, কখন খুলল? কে ঢুকল, কীভাবে ঢুকল, কখন ঢুকল? কার বা কাদের সাহায্যে ঢুকল? আর খুনটা করার পর অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরল কীভাবে…
—গেটে রাতের সিকিউরিটি গার্ডরা তো বলছে, কাউকে বেরতে দেখেনি…
—হ্যাঁ .. বেরতে গেলেও গেট পাস লাগত… খুনটা করার পর পালাতে তো হবে, পালাল কীভাবে…
—সার্ভেন্টস কোয়ার্টার সার্চ করেও তো কিছু পাওয়া যায়নি বলছ?
—না স্যার। মিলছে না, কিছুতেই মিলছে না ফ্ল্যাটে খুনি বা খুনিদের ঢোকা-বেরনোর অঙ্কটা… মিলছে না… কিছু একটা মিস করছি নির্ঘাত।
আশিকের চিন্তিত চেহারাটা দেখে একটু খারাপই লাগে ওসি হোমিসাইডের। এই ঠান্ডা মাথার স্থিতধী অফিসারটিকে তিনি বিশেষ স্নেহের চোখে দেখেন। চেয়ার ছেড়ে উঠে পিঠে আশ্বাসের হাত রাখেন।
—মিলবে, ঠিক মিলবে। সবে তো একটা দিন হয়েছে। আকাশ থেকে উড়ে এসে তো কেউ রান্নাঘরের দরজা খোলেনি। আততায়ী বা আততায়ীরাই খুলেছে। এখন প্রশ্ন হল, কীভাবে খুলেছে? আর কীভাবে ঢুকেছে?
—স্যার…
—একটা কথা বলি শোনো তোমায়। আমরা যখন ব্যারাকপুরের পুলিশ ট্রেনিং কলেজে প্রবেশনার ছিলাম, একজন আইপিএস অফিসার গেস্ট লেকচারার হিসেবে ইনভেস্টিগেশনের উপর একটা ক্লাস নিয়েছিলেন। শার্লক হোমসের রেফারেন্স দিয়েছিলেন একটা। নোট করে নিয়েছিলাম। মনে গেঁথে আছে এখনও।
—কী স্যার?…
—আর্থার কোনান ডয়েলের একটা উপন্যাস আছে, পড়েছ কিনা জানি না, ‘The Sign of the Four’। যেখানে হোমস এক জায়গায় বলছেন, ‘When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth.’
—স্যার….
—যা যা অসম্ভব, যা যা হতেই পারে না, সেগুলো একটা একটা করে বাদ দাও। যা পড়ে থাকবে, সেটা যতই কল্পনাতীত মনে হোক, সত্যি হতে বাধ্য। এক্ষেত্রেও যা যা অসম্ভব, বাদ দাও একটা একটা করে। এই এলিমিনেশনটা করতে সময় লাগবে, কিন্তু ধৈর্য হারিয়ো না। একটা সময় দেখবে, যেটা ভাবোইনি কখনও, সেটাই আসলে ঘটেছে। সেটাই সত্যি!
আশিক শোনেন চুপচাপ। মাথা নেড়ে বেরিয়ে আসেন। ফের গন্তব্য আলিপুর। যেতে যেতে ভাবেন, আবাসনের পুরো কম্পাউন্ডটা আঁতিপাঁতি করে তল্লাশি করা হয়েছিল ঘটনার দিন। কিছুই পাওয়া যায়নি। গল্পের গোয়েন্দা হলে নির্ঘাত খুঁজে পেতেন আধপোড়া সিগারেটের টুকরো, কাদায় পায়ের ছাপ কিংবা নিদেনপক্ষে কোনও হুমকি-চিরকুট! কল্পনার শার্লক হোমসের তত্ত্বকথা শুনতে ভাল। বাস্তব অনেক রুক্ষ জমির।
জিজ্ঞাসাবাদ আজও সারাদিন ধরে চালিয়ে যাওয়াই যায়। চালাতে হবেও। কিন্তু ‘লিড’ তো দরকার একটা এগোনোর। কাউকে চেপে ধরতে গেলে, সে বাড়ির লোকই হোক বা কাজের লোক, একটা সূত্র তো দরকার। সেটা কোথায়?
সূত্র অমিলই থাকল। তথ্যসংগ্রহের কাজ যা যা বাকি ছিল, করলেন আশিক। আবাসনের বাসিন্দাদের অনেকের সঙ্গে কথা বললেন দীর্ঘক্ষণ। অজানা কোনও তথ্য আর উঠে এল কই?
১৩ তারিখ রাত্রে আবাসন থেকে বেরনোর সময় ইলেকট্রনিক মিডিয়ার জনাকয়েক সাংবাদিক ছুটে এসে ‘বুম’ ধরলেন আশিকের মুখের সামনে। পাশ কাটিয়ে গাড়িতে ওঠার সময় আশিক শুনতে পেলেন, ‘আপনারা দেখলেন দিনভর তদন্তের পর ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের অফিসাররা বেরিয়ে এলেন অ্যাপার্টমেন্ট থেকে। আমাদের প্রশ্নের উত্তরে মুখে কুলুপ এঁটেছে পুলিশ। খুনের পর প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা হতে চলল, অথচ …’
পরের দিন, ১৪ অগস্টের দুপুরে যখন শ্রীনিকেত-এ পৌঁছলেন আশিক, ততক্ষণে আটচল্লিশ ঘণ্টা সত্যিই পেরিয়ে গিয়েছে ললিতা-হত্যার পর। ছুটিতে থাকা দুই কাজের লোক ফিরে এসেছেন। অমলেশ দুপুরে। রাজেশ বিকেলের দিকে। যাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করে নতুন কিছু পাওয়া গেল না। অন্যরা যা বলেছিলেন, ওঁরাও তাই বললেন… ললিতার ব্যবহার মাঝেমাঝে রুক্ষ হলেও আদতে সহৃদয় প্রকৃতির মহিলা ছিলেন।
অমলেশের গলা বুজে এল ললিতার কথা বলতে গিয়ে।
—আমার স্ত্রী-র অপারেশনের জন্য ছুটিতে গিয়েছিলাম। হাজার তিরিশেক টাকার মতো খরচ হত। দিদা বলে ডাকতাম ওঁকে। ধার চেয়েছিলাম কিছু। পাঁচ হাজার এক কথায় দিয়ে দিয়েছিলেন।
—কোথায় অপারেশন হল স্ত্রী-র? কী অসুখ?
—মধ্যমগ্রামের নার্সিংহোমে স্যার। গলব্লাডারে স্টোন। পেটে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছিল। এখন ঠিক আছে।
রাজেশও কেঁদে ফেললেন ‘মা-জি’-র কথা বলতে গিয়ে।
—মা-জি আমাকে ছেলের মতো ভালবাসত। বকাঝকা করলে পরে গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিত। কলকাতার বাইরে তীর্থে গেলে আমি সঙ্গে যেতাম। আমাকে ছাড়া যেতই না। হিন্দি সিনেমা দেখতে আমি খুব ভালবাসি। নতুন ছবি রিলিজ় হলে নিজে টাকা দিত টিকিটের। বসুশ্রীতে অজয় দেবগনের ‘Yuva’ দেখার টাকা দিয়েছিল এই তো গত মাসে।
দ্বিতীয় দফার জেরায় ত্রিলোকি তথ্য দিলেন আর একটা। গৃহকর্মী সীতার সঙ্গে নাকি লিফটম্যান লক্ষ্মণের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল ইদানীং। প্রায়ই লক্ষ্মণ এই ফ্ল্যাটে আসত। যেটা ললিতা বিন্দুমাত্র পছন্দ করতেন না। সীতাকে নাকি সপ্তাহখানেক আগে এ নিয়ে বকাঝকাও করেছিলেন। লক্ষ্মণকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলেছিলেন চেঁচিয়ে। এই ব্যাপারটার আরও গভীরে যাবেন, ঠিক করলেন আশিক। প্রেমে বাধা বড় বিপজ্জনক জিনিস। প্রণয়ী-প্রণয়িনীর হিতাহিত জ্ঞান লোপ পায় অনেক সময়। তেমন কিছু ঘটেছিল?
সন্ধে হয়ে গেল প্রশ্নোত্তর-পর্ব মিটতে মিটতে। আলিপুর কোর্টের অ্যাডভোকেটের সঙ্গে ওঁর ভবানীপুরের বাড়িতে দেখা করতে আশিক বেরলেন সাড়ে পাঁচটা নাগাদ। তার আগে সুনীল গোয়েঙ্কাকে এক প্রস্থ জিজ্ঞাসাবাদ হয়ে গেছে। সুনীলের কথাবার্তায়, আচার-আচরণে কণামাত্র অস্বাভাবিকতা খুঁজে পাননি আশিক। মায়ের এহেন মৃত্যুতে পুত্রের যেমন শোকগ্রস্ত হওয়ার কথা, তেমনই। আশিকও তোলেননি ‘প্রোবেট’-এর কথা। আগে দেখা যাক ওই উকিলের সঙ্গে কথা বলে, সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারটা কতটা এগিয়েছে, আদৌ এগিয়েছে কি না।
হাজরা মোড়ের সিগন্যালে গাড়ি থামল। দু’ মিনিট গেল, চার মিনিট গেল, থেমেই আছে। কী ব্যাপার? গাড়ি থেকে নেমে একটু এগিয়ে গিয়ে দেখে এল ড্রাইভার।
একটা বড় মিছিল যাচ্ছে স্যার। ট্র্যাফিক সার্জেন্ট বললেন, গাড়ি ছাড়তে কম করে হলেও আরও মিনিট দশ।
অপেক্ষা ছাড়া কী আর করার? আশিক আনমনা তাকিয়ে থাকেন গাড়ির বাইরে। বসুশ্রীর ইভনিং শো শুরু হওয়ার মুখে। লোক ঢুকছে। সিনেমার পোস্টারের দিকে তাকান আশিক। ‘Yuva’.. starring Ajay Devgan, Abhishek Bachchan..।
এই ছবিটার কথাই বলছিল রাজেশ ছেলেটা। অজয় দেবগনের ফ্যান, কোনও ছবিই নাকি মিস করে না। নিজের ওই বয়সটার কথা মনে পড়ে আশিকের। অমিতাভ বচ্চনের একটা ছবিও মিস করতেন না তখন। এখনও করেন না। বিগ বি-র কত ছবি যে এই বসুশ্রীতেই দেখেছেন। তবে এই হলে দেখা যে ছবিটা মনে সবচেয়ে বেশি দাগ কেটেছিল, তার প্রতিটা দৃশ্য এখনও মুখস্থ বলতে পারবেন। ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’।
মিছিল হাজরা মোড় পেরিয়ে গেছে। সিগন্যাল গাঢ় সবুজ। গাড়িঘোড়া চলতে শুরু করেছে ফের। যখন গাড়ি যদুবাবুর বাজার পেরোচ্ছে, হঠাৎই আশিক তরঙ্গস্রোত টের পান মস্তিষ্কের ধূসর কোষগুলোয়। যাকে Hercule Poirot বলতেন, ‘the little grey cells’।
—এই, গাড়ি ঘোরাও!
ড্রাইভার অবাক দৃষ্টিতে তাকান পিছন ফিরে। অধৈর্য আশিক ফের নির্দেশ দেন।
—বলছি তো গাড়ি ঘোরাও!
গাড়ি ফের দক্ষিণমুখী। থেমেছে গিয়ে সেই হাজরা মোড়েই। আশিক সোজা গিয়ে ঢুকেছেন বসুশ্রীতে, ম্যানেজারের ঘরে। পুলিশ দেখে ম্যানেজার সামান্য হতচকিত। উঠে পড়েছেন চেয়ার ছেড়ে।
—কী ব্যাপার স্যার?
—তেমন কিছু না, একটা ব্যাপার জানার ছিল।
—বলুন না স্যার… আপনার জন্য চা-কফি কিছু…
—না না, দরকার নেই… সামান্য ব্যাপার… আচ্ছা, এই ‘Yuva’ বলে সিনেমাটা কতদিন ধরে চলছে এখানে?
—এই তো গত সপ্তাহ থেকে স্যার, মানে গত শুক্রবার ৬ তারিখ থেকে। রিলিজ় হয়েছে মাসদুয়েক আগে। অন্য একটা ছবি ভাল চলছিল। ‘Yuva’ লেগেছে গত সপ্তাহ থেকে।
আশিকের হৃদ্স্পন্দন বেড়ে যায় হঠাৎ। তা হলে কি যা ভাবছেন, তা-ই? আজ শনিবার, ১৪ তারিখ। ছবি রিলিজ় করেছে ৬ তারিখ। মানে বসুশ্রীতে ছবিটা দেখতে গেলে ৬ থেকে ১৩-র মধ্যে দেখতে হবে রাজেশকে। রাজেশ ছুটিতে ওড়িশা গিয়েছিল ৮ তারিখ। ফিরেছে আজ বিকেলে। তা হলে ছবিটা দেখল কবে? যদি ছয় বা সাত তারিখে দেখে না থাকে, তা হলে ৮ থেকে ১৩-র মধ্যে দেখেছে। কিন্তু বলল তো গত মাসে বসুশ্রীতে দেখেছে! কী করে সম্ভব? ছুটিতে ওড়িশায় যাওয়ার গল্পটা তা হলে ডাহা মিথ্যে? ওই সময়টার মধ্যে কোনও একদিন অন্তত কলকাতায় ছিল? বাবার অসুখের নাম করে ছুটি নিয়ে কেন ছিল শহরে? মিথ্যে বলল কেন? যার একটা মিথ্যে ধরা পড়ে গেছে, তাকে আর বিশ্বাস করা চলে না।
যতটা না সমাপতন, তার থেকে ঢের বেশি কাজ করেছিল তদন্তকারীর সহজাত অনুসন্ধিৎসু প্রবৃত্তি। গাড়িতে ফিরতে ফিরতে বসুশ্রীতে দেখা ‘জয় বাবা ফেলুনাথ’ স্মৃতিতে ফিরে এসেছিল আশিকের, প্রিয় সেই দৃশ্যটা চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল হঠাৎ, মনে পড়েছিল সংলাপটা। এবং মনে পড়তেই যদুবাবুর বাজারের কাছে গাড়ি থামিয়ে দিয়েছিলেন আশিক, ড্রাইভারকে বলেছিলেন গাড়ি ঘোরাতে।
ছবিটা যখন দেখেছিলেন, তখন বোধহয় ক্লাস নাইন বা টেন। শেষ দৃশ্যে মছলিবাবার বেশধারী ফেলুদা নয়, মগনলালের ডেরায় লালমোহনবাবুর দিকে তাক করে সেই ‘knife throwing’-এর দমবন্ধ করা সিনটাও নয়, কিশোর আশিকের সবচেয়ে ভাল লেগেছিল ছবির অন্য একটা জায়গা। যেখানে ঘোষালবাড়ির কর্মী বিকাশের মিথ্যে ধরে ফেলেছিল ফেলুদা। একটা নির্দিষ্ট সময়ে কোথায় ছিলেন, জানতে চাওয়ায় বিকাশ বলেছিলেন, গান শুনছিলেন রেডিয়োতে। আখতারি।
ফেলুদার সন্দেহ হওয়াতে যাচাই করেছিল আকাশবাণীর প্রোগ্রাম তালিকা থেকে। ওইসময় আখতারি হচ্ছিলই না। আশিকের দারুণ লেগেছিল মিষ্টির দোকানে ফেলুদার চেপে ধরা বিকাশকে, কোমরে আগ্নেয়াস্ত্র ঠেকিয়ে নিয়ে যাওয়া যন্তরমন্তরের ছাদে, সেই সংলাপ সহ, ‘যার একটা মিথ্যে ধরা পড়ে গেছে, তাকে আর বিশ্বাস করা চলে না।’
রাজেশেরও একটা মিথ্যে ধরা পড়ে গেছে, তাকেও আর বিশ্বাস করা চলে না। উকিলের বাড়ি আর যাওয়া হল না আশিকের। গাড়ি ঘুরিয়ে সোজা ‘শ্রীনিকেত অ্যাপার্টমেন্টস’। রাজেশ ছিল ছাদের সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে। আশিক এগারো তলায় নামিয়ে আনলেন। কোন ভণিতা না করে চোখে চোখ রাখলেন রাজেশের।
—Yuva সিনেমাটা কেমন লেগেছিল?
হঠাৎ এ প্রশ্নে কিছুটা থতমত খেয়ে যায় রাজেশ।
—মানে?
—বলছি, কেমন লেগেছিল?
—ভাল স্যার…
—কবে দেখলি?
—এই তো গত মাসে স্যার। আপনাকে বললাম তো বিকেলে, বসুশ্রীতে।
আর কিছু জিজ্ঞাসা করার ছিল না আশিকের। কলার চেপে ধরে হিড়হিড় করে ফ্ল্যাটের বাইরে লিফটে। নীচে নেমে গাড়িতে তুলে সোজা লালবাজার। গাড়িতে একটা শব্দও ব্যয় করলেন না আশিক। বেশ বুঝতে পারছিলেন, ঘামতে শুরু করেছে পাশে বসা রাজেশ। মুখচোখ থেকে ব্লটিং পেপার দিয়ে যেন রক্ত শুষে নিয়েছে কেউ।
কতশত ধুরন্ধর অপরাধীর লালবাজারের ইন্টারোগেশন রুমে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে যেতে দেখেছেন আশিক, ইয়ত্তা নেই। তুলনায় এ ছোকরা তো নেহাতই চুনোপুঁটি! হাতি-ঘোড়া যেখানে তলিয়ে যায়, মশা সেখানে কী করে জল মাপবে? খুচরো চড়-থাপ্পড় খরচ হল একটা-দুটো, এবং বলতে শুরু করল রাজেশ। গোয়েন্দারা শুনতে থাকলেন ললিতাদেবীর হত্যার রুদ্ধশ্বাস নেপথ্যকথা।
—আমার বাবার কোনও অসুখ-টসুখ হয়নি স্যার। গ্রামের বাড়ির এক বন্ধুকে বলেছিলাম, যে বাড়িতে কাজ করি, সেখানে ছুটি কিছুতেই দিতে চায় না। তুই ফোন করে বলবি, বাবার অসুখ। তা হলে এক সপ্তাহের জন্য বাড়ি আসতে পারব।
—তারপর?
—স্যার, বাড়িতে আমি যাইনি। নরেন্দ্রপুরে আমাদের এক দূরসম্পর্কের মাসি থাকেন। বউবাজারে একটা বাড়িতে কাজ করেন। ওঁর বাড়িতে গিয়ে উঠেছিলাম আট তারিখ। আমাকে ঘরের চাবি দিয়ে মাসি সকালে বেরিয়ে যেত কাজে। আমি বেরলে চাবিটা জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে কাছের একটা টেবিলের উপর রেখে দিতাম। আমার ফেরার আগে মাসি চলে এলে হাত ঢুকিয়ে চাবিটা নিয়ে দরজা খুলত।
—বেশ ..
—পরের দিন, ভবানীপুরের একটা দোকান থেকে একটা ভিআইপি সুটকেস কিনলাম। তার পরের দিন Yuva দেখলাম বসুশ্রীতে। এগারো তারিখ ভোরে অ্যাপার্টমেন্টে ঢুকলাম।
—এগারো তারিখ ভোরে?
—হ্যাঁ স্যার, এগারো তারিখ।
—কীভাবে ঢুকলি?
—স্যার, গেট দিয়ে ঢুকতে পারব না জানতাম। নাইটগার্ড দু’জনের একজন জেগে থাকত, একজন ঘুমোত পালা করে। গেটে তালা দিয়ে রাখত রাত বারোটার পর। ঢোকার রাস্তা ছিল না।
—তা হলে?
—বাড়িটার চারদিকে বেশ কিছু উঁচু গাছ আছে, নিশ্চয়ই দেখেছেন স্যার। পশ্চিম দিকে বেশি। আমি আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলাম, গাছে উঠে ওখান দিয়ে পাঁচিল টপকাব। টপকে বাড়ির ভিতর যাওয়ার সময় পাঁচিলের তারে লেগেছিল পায়ে।
—দেখা …কোথায় লেগেছিল?
ট্রাউজার হাঁটু অবধি তুলে ক্ষতচিহ্ন দেখায় রাজেশ। ফের বলতে শুরু করে।
—ওই সময়টায় লিফটম্যান থাকে না, কেয়ারটেকারের অফিসের সামনে খাটিয়ায় অচ্ছেবর ভাইয়া ঘুমিয়ে থাকে। কেউ কোত্থাও থাকে না। সোজা সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম ছাদে। অন্য কাজের লোকেরা তখন সবাই ঘুমোচ্ছে।
—তারপর?
—ছাদে উঠে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এগারো তলার রান্নাঘরের সামনে নেমে এলাম। জানতাম, মা-জি ভোরে উঠবে। পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ দরজা খুলে দিয়ে পুজোয় বসবে। সাড়ে ছ’টা পর্যন্ত ঠাকুরঘরে পুজো করবে। বারান্দা থেকে কালীঘাট মন্দিরের চুড়ো দেখা যেত। পুজো শেষ হলে দশ মিনিট বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওদিকে তাকিয়ে প্রণাম করত মা-জি। দরজা খুলে গেল সাড়ে পাঁচটায়। মিনিট দশেক অপেক্ষা করে ঢুকে পড়লাম ভিতরে।
—হুঁ…
—বসার ঘরে এসে হলঘরের কোনায় যে বাথরুমটা সবসময় বন্ধ থাকত, সেটার ছিটকিনি খুলে ঢুকে পড়লাম। ভিতর থেকে বাথরুমের দরজা বন্ধ করে দিলাম।
—বাথরুমে?
—লুকোনোর ওটাই সবচেয়ে ভাল জায়গা ছিল স্যার। ওই বাথরুমটা বহু বছর ব্যবহার হয় না। ওর মধ্যে কেউ থাকতে পারে, কেউ ভাবতেও পারবে না, জানতাম।
—তারপর?
—ভেবেই রেখেছিলাম, খুনটা রাতে করে পরদিন ভোরে বেরিয়ে যাব। সারাদিন ওই বাথরুমেই থাকলাম।
আশিক এবং সঙ্গীরা স্তব্ধ হয়ে যান। বলে কী! এভাবেও প্ল্যান করা যায়!
—সঙ্গে একটা চটের ব্যাগ ছিল। মাসির বাড়ি থেকে একটা বড় কাঠ কাটার ছুরি এনেছিলাম। দু’প্যাকেট বিস্কুট আর কয়েকটা টিফিন কেকও এনেছিলাম। সারাদিনে ওগুলো খেলাম। বাথরুমেই ঘুমোলাম। একটুও সাড়াশব্দ করিনি সারাদিন। অপেক্ষা করে থাকলাম রাতের জন্য।
—বলতে থাক…
—রাত যখন তিনটে, বাথরুম থেকে বেরলাম। মা-জি নিজের শোবার ঘরে ঘুমোচ্ছে। বারান্দায় লোহার পাইপ রাখা ছিল কয়েকটা। একটা নিলাম। আগে মা-জি র মুখ চেপে ধরলাম। জেগে গেল। আমার জামাটা চেপে ধরল। টানাহ্যাঁচড়া হল। পাইপ দিয়ে মা-জির মাথায় মারলাম জোরে। রক্ত বেরচ্ছিল খুব। বেডশিট দিয়ে মুড়লাম মা-জিকে। টেনে টেনে নিয়ে গেলাম। ড্রয়ারে স্টোররুমের চাবি থাকত। সেটা দিয়ে স্টোররুম খুলে ঢোকালাম বডিটাকে।
—হুঁ…
—মা-জির তখনও নিশ্বাস পড়ছিল। ভয় পেয়ে গেলাম, তা হলে কি মরেনি? ছুরিটা চালালাম গলায়। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরতে লাগল। একটু পরে নাকে হাত দিয়ে দেখলাম, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে।
—এরপর আলমারি খুললি, টাকাপয়সা নিলি, ব্যাগে ভরলি…
—হ্যাঁ স্যার, বেরিয়ে এলাম রান্নাঘর দিয়ে। ছাদে উঠে আবার সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলাম। যেভাবে ঢুকেছিলাম, সেভাবেই বেরলাম। পাঁচিল টপকে। চটের ব্যাগটা আগে ছুড়ে বাইরে ফেললাম। তারপর দেওয়াল টপকে বেরিয়ে এলাম। তখন ভোর পাঁচটা সোয়া পাঁচটা হবে।
—তারপর?
—নরেন্দ্রপুরে মাসির বাড়িতে এলাম। মাসি তখন কাজে বেরিয়ে গেছে। ভিআইপি-তে টাকাপয়সা ভরে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরলাম ওড়িশার। পরদিন খুব ভোরে পৌঁছলাম। বাড়িতে সুটকেসটা রেখে এসেছি। বাড়িতে বললাম, একদিনের জন্য এসেছি। ত্রিলোকিদা বিকেলে ফোন করল। বলল, পুলিশ চলে আসতে বলছে। মা-জি খুন হয়ে গেছেন। আমি গতকাল বিকেলের ট্রেন ধরে আজ কলকাতা চলে এলাম।
—স্টোররুমের চাবিটা?
—কয়েকটা বাড়ি পরে একটা ঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়েছি। চলুন স্যার, দেখিয়ে দিচ্ছি।
—সে তো যাবই, কিন্তু তোকে তোর মা-জি এত ভালবাসতেন, মারলি কেন?
—টাকার লোভে স্যার। বারোশো টাকা মাইনে পেতাম স্যার। ওতে কিছু হয়? সিনেমায় দেখতাম বড়লোকরা কীভাবে জীবন কাটায়। কত মস্তি। ভাবতাম, সারাটা জীবন কি এই চাকরগিরি করেই কেটে যাবে? কিছুদিন পরে সব ঠান্ডা হয়ে গেলে চাকরিটা ছেড়ে দেব ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম, টাকাটা দিয়ে ব্যবসা শুরু করব কিছু।
রাতেই আশিকের নেতৃত্বে রাজেশকে নিয়ে টিম রওনা দিল ওড়িশায়। গ্রামের বাড়ি থেকে উদ্ধার হল সেই ভিআইপি সুটকেস। যার মধ্যে ভরতি টাকার বান্ডিল। সব মিলিয়ে এক লক্ষ আটান্ন হাজার। পাওয়া গেল রক্তমাখা শার্ট, যার দুটো বোতাম নেই। কলকাতায় ফিরে রাজেশের বয়ান অনুযায়ী অশোকা রোডের ফুটপাথ সংলগ্ন একটা ঝোপ থেকে পাওয়া গেল স্টোররুমের সেই চাবি। ফরেনসিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হল, রাজেশের ওড়িশার বাড়ি থেকে পাওয়া শার্টের বোতাম আর ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া দুটো বোতাম একই পোশাকের। কী বাকি থাকে আর পারিপার্শ্বিক প্রমাণের? কী বাকি থাকে আর অভিযুক্তের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার?
শাস্তি হয়েছিল যাবজ্জীবন কারাবাসের। আশিকের তদন্ত প্রশংসা কুড়িয়েছিল আদালতের।
মার্ডার ফর গেইন। টাকার জন্য খুন। লাভের জন্য খুন। লাভ কি হয় আদৌ? হয় ‘গেইন’ আদৌ?
আইন তো যথাসময়ে এসে কড়া নাড়েই দরজায়।
পুনশ্চ: অনিল এবং সুনীল, এই নামদুটি পরিবর্তিত।
২.০৭ বিপুলা এ পৃথিবীর যতটুকু জানি
[বিনোদ বর্মণ হত্যা
সুশান্ত ধর, সহ নগরপাল, গোয়েন্দাবিভাগ। ২০০৪ সালে পেয়েছেন ভারত সরকারের ‘ইন্ডিয়ান পুলিশ মেডেল’। ২০১১ সালে সম্মানিত হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর ‘প্রশংসা পদক’-এ।]
—বাবা!
নিস্তব্ধতা ভেঙে একটা আর্তচিৎকার। তারপর হাঁটু মুড়ে মাটিতেই বসে পড়ে অঝোর কান্না। পোড়খাওয়া পুলিশ অফিসাররাও থামাতে পারছিলেন না তিরিশ বছরের যুবককে। যাঁর বাবার দেহ ততক্ষণে বাইরে আনা হয়েছে মাটি খুঁড়ে। যুবক কেঁদে চলেছেন জন্মদাতার দেহ আঁকড়ে ধরে।
‘দেহ’ মানে যতটুক অবশিষ্ট রয়েছে আর। পচন ধরেছে। কাদামাটির প্রলেপ সর্বাঙ্গে। বালতি বালতি জল দিয়ে ধুয়েমুছে কিছুটা পরিষ্কার হল অবয়ব। দেখে যতটা আন্দাজ করা যায়, মৃতের বয়স ষাটের কাছাকাছি হবে। হাফ প্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে। মাথার বাঁ দিকে দুটো গভীর ক্ষত। মুখ বাঁধা একটুকরো কাপড় দিয়ে। গলায় ফাঁসের দাগ স্পষ্ট। ডান হাতে উল্কিতে আঁকা ত্রিশূল। বাঁ হাতের উল্কিতে লেখা, ‘বিনোদ’।
কালীঘাট থানার বড়বাবু মোবাইল বার করেন পকেট থেকে। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টকে এখনই জানানো দরকার। ফোনে ধরেন ওসি হোমিসাইডকে।
—স্যার, বডি রিকভার্ড হয়েছে একটা। সেমি-ডিকম্পোজ়ড। ঈশ্বর গাঙ্গুলি স্ট্রিটে। মাটির নীচে পোঁতা ছিল। গলায় ‘লিগেচার মার্ক’ আছে। হেড ইনজুরি ভিজিবল। মার্ডার।
ফোন রেখে দুটো কাজ করেন ওসি হোমিসাইড। এক, ডিডি-র ফটোগ্রাফি সেকশনে নির্দেশ, ফটোগ্রাফার যাতে যত দ্রুত পৌঁছে যায় স্পটে। দুই, ফরেনসিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির ডিরেক্টরকে ফোন করে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে অনুরোধ, ‘স্যার, একটা টিম যদি তাড়াতাড়ি পাঠানো যায়, দেখুন প্লিজ়।’
পরের কাজ বলতে গোয়েন্দাপ্রধানকে খবরটা জানানো এবং দু’-তিনজন সহকর্মীকে নিয়ে তড়িঘড়ি গাড়িতে উঠে বসা। ড্রাইভার গৌতম গাড়ি স্টার্ট দিতে দিতে হাতঘড়ির দিকে তাকান। বিকেল চারটে। মানে,আজ বাড়ি ফিরতে ফিরতে হয়তো মাঝরাত হয়ে যাবে।
বহু বছর হয়ে গেল হোমিসাইড বিভাগের গাড়ি চালাচ্ছেন। ওসি যখন এত হন্তদন্ত হয়ে গাড়িতে উঠে বসছেন, নির্ঘাত খুন হয়েছে কোথাও। এবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে তদন্ত চলবে। লালবাজারের কর্তারা আসবেন একে একে। সন্ধে পেরিয়ে রাত গড়িয়ে যাবে। সারারাত বাড়ি ফেরা হয়নি, গাড়ি নিয়ে ছুটতে হয়েছে টালা থেকে টালিগঞ্জ, এমন যে কত হয়েছে এতদিনের চাকরিতে। কে জানে আজ কপালে কী আছে?
লালবাজারের গেট পেরিয়ে ডানদিকে টার্ন নিতে নিতে জিজ্ঞেস করেন গৌতম।
—কোথায় স্যার?
—কালীঘাট। হরিশ মুখার্জি রোড ধরো, তাড়াতাড়ি হবে। থানার কাছেই।
থানার কাছে বলেই চাঞ্চল্য আরও বেশি। গাড়ি ঢুকতেই পারল না ঈশ্বর গাঙ্গুলি স্ট্রিটে। আটকে গেল। সরু রাস্তায় জমাট ভিড় স্থানীয় মানুষের। ঠেলেঠুলে ওসি হোমিসাইডকে রাস্তা করে দিলেন কালীঘাট থানার এক কনস্টেবল, যাঁর মুখে রুমাল চাপা দেওয়া, ‘আসুন স্যার, বড়বাবু আর বাকিরা বাড়ির ভিতরে। যা দুর্গন্ধ, টেকা যাচ্ছে না।’
টেকা যে মুশকিল, গলিতে ঢুকতে ঢুকতেই টের পেয়েছিলেন ওসি হোমিসাইড। অবাক হননি। ফোনে তো জেনেইছেন, বডি সেমি-ডিকম্পোজ়ড। পচতে থাকা মনুষ্যদেহের গন্ধে অন্নপ্রাশনের ভাত মুখে উঠে আসারই কথা। বাড়ির ভিতরে ঢুকে যখন ‘বডি’-র উপর চোখ রাখলেন প্রথম, তখনও মৃতদেহের পাশে বসে আছাড়িপিছাড়ি কেঁদে চলেছেন যুবক। ফটোগ্রাফার এসে গেছেন। দেহের ছবি উঠছে বিভিন্ন দিক থেকে। শাটার টেপার ‘ক্লিক ক্লিক’ আওয়াজ ঢাকা পড়ে যাচ্ছে সদ্য পিতৃহারার বিলাপে।
.
বিনোদ বর্মণ হত্যা মামলা। কালীঘাট থানা। কেস নম্বর ১৫৬, তারিখ ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০০৫। ধারা, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ এবং ২০১। খুন এবং প্রমাণ লোপাট।
২০/৩/সি ঈশ্বর গাঙ্গুলি স্ট্রিটের একটি তালাবন্ধ বাড়ি থেকে দুর্গন্ধ বেরচ্ছে, ফোনে খবর এসেছিল কালীঘাট থানায়। থানার খুব কাছেই ওই রাস্তা। দূরত্ব খুব বেশি হলে আড়াইশো মিটার। ওসি পৌঁছলেন দ্রুত।
একটা ছোট একতলা পাকা বাড়ি। ঢোকার মুখে লোহার গ্রিল। যাতে তিনটে তালা ঝুলছে। ঘরের মধ্যে ঢোকার দরজা গ্রিলের পিছনে। সেই দরজাতেও তালা ঝুলছে একটা। কৌতূহলী জনতা ভিড় জমিয়েছে বাড়ির সামনে।
কার বাড়ি? স্থানীয় মানুষের থেকে জানা গেল, বাড়ির মালিকের নাম বিনোদ বর্মণ। এই বাড়িটা কিনেছেন বছরের শুরুর দিকে। তবে এখানে থাকেন না। কোথায় থাকেন? কালীঘাট শ্মশানের কাছে হিউম রোডে। এক অফিসার সঙ্গে সঙ্গেই গেলেন হিউম রোডে। এবং মিনিট কুড়ির মধ্যে ফিরলেন বছর তিরিশের এক যুবককে নিয়ে। কে ইনি? রাজেশ বর্মণ, এই বাড়ির মালিক বিনোদের একমাত্র ছেলে। পেশায় অটোচালক। বাড়ির সামনে ওই ভিড়ভাট্টা আর ভিতর থেকে দুর্গন্ধের বহর দেখে দৃশ্যতই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন রাজেশ। হাত চেপে ধরেন ওসি-র।
—স্যার, বাবা গত ২৫ তারিখ বেলা ১১টা নাগাদ আমাদের হিউম রোডের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেনি। বাবা রোজ সকালে ঘণ্টাখানেকের জন্য এখানে আসত দেখভাল করতে। তারপর ব্যবসার কাজ সেরে রাতে ফিরত। সে-রাতে ফেরেনি দেখে এখানে এসেছিলাম খোঁজ করতে। তালা বন্ধ ছিল। আমরা ভাবছিলাম, হয়তো ব্যবসার জরুরি কোনও কাজে কলকাতার বাইরে গেছে। মাঝেমাঝেই যেতে হত। কিন্তু পরের দিনও যখন ফিরল না, তখন মিসিং ডায়েরি করেছি আপনাদের থানায়। রাতের দিকে। খুব ভয় করছে স্যার।
—তালাগুলোর ডুপ্লিকেট চাবি আছে আপনাদের বাড়িতে?
—না স্যার, চাবি এক সেটই ছিল। বাবা নিজের কাছে রাখত।
ওসি তাকান সঙ্গী সাব-ইনস্পেকটরের দিকে। যিনি বোঝেন, এখন কী করণীয়। তালাটা ভাঙতে হবে।
ভাঙা হল গ্রিলে লাগানো তিনটে তালা। ভিতরের দরজার তালাও। পুলিশ ঢুকল ভিতরে। দু’কামরার বাড়ি। একটা বাথরুম। আসবাবপত্র বিশেষ নেই। চেয়ার-টেবিল একটা করে, খাট একটা। যাতে সাদামাটা বেডশিট আর একটা বালিশ শুধু। বেশ বোঝা যায়, বাড়ি ফাঁকাই পড়ে থাকত। নিয়মিত বসবাস করত না কেউ। ব্যবহৃত হত না খাট-বিছানা।
গন্ধের উৎসের হদিশ ঘরে মিলল না। মিলল বাড়ির পিছন দিকে। বাউন্ডারি ওয়াল আর ঘরের গাঁথনির মাঝে একফালি লম্বা জায়গায়। যার একটা অংশে মাটি আলগা হয়ে আছে। উপরে থিকথিক করছে পোকা।
খোঁড়ার ব্যবস্থা করতে আধঘণ্টার মতো লাগল। মাটি কাটার লোক ডাকা হল। জোগাড় হল কোদাল-শাবল-ঝুড়ি। মাটি একটু খুঁড়তেই বেরল এক পুরুষের মৃতদেহ। কাদামাটি মাখা সারা শরীরে। পলকের দেখাতেই চিনলেন রাজেশ। দু’হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়লেন মাটিতে।
—বাবা!
ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা এলেন। খুঁটিয়ে দেখলেন সব। জানালেন, যা বোঝা যাচ্ছিল সাদা চোখেও। খুনি বা খুনিরা গর্ত যেটা খুঁড়েছিল, সেটা গন্ধ ঢাকা দেওয়ার মতো গভীর ছিল না। আড়াই ফুট বাই ছয়-সাত ফুটের মতো খুঁড়ে মৃতদেহ শুইয়ে দেওয়া হয়েছিল। তারপর মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল আলগা ভাবে, তাড়াহুড়োয়। প্রমাণ লোপাটের কাজটা মোটেই পরিপাটি হয়নি। গর্তটা যদি আরও বেশ কিছুটা গভীরে খোঁড়া হত লম্বায়-চওড়ায়, সময় নিয়ে উপরে পর্যাপ্ত মাটি চাপা দেওয়া হত, পচনশীল দেহের গন্ধ এভাবে ছিটকে আসত না বাইরে। পচেগলে মাটির সঙ্গে মিশে গিয়ে একটা সময়ের পর পড়ে থাকত হাড়গোড়।
অপরাধের ঘটনাস্থল আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে দেখাটা তদন্তের গোড়ার কথা। সবাই জানে। তবে ওই গোড়ার রুটিনমাফিক কাজটায় এতটুকু ঢিলে দেওয়ার বিলাসিতা দেখানো যায় না। দেখালে ভুগতে হয় চার্জশিট দেওয়ার সময়। অপরাধের কিনারা করে ফেলেও হিমশিম খেতে হয় প্রমাণ জোগাড়ে। যে প্রমাণ হয়তো নাগালের মধ্যেই থাকত, ‘প্লেস অফ অকারেন্স’-এর তল্লাশিতে আরও বেশি মনোযোগী হলে।
মনোযোগে খামতি রাখল না পুলিশ। সন্ধে হয়ে গেছে। ড্রাগন লাইট নিয়ে ওসি হোমিসাইড আঁতিপাঁতি তল্লাশি শুরু করলেন বাড়ির। ‘কষ্ট করলে কেষ্ট’ বলতে মিলল একটা প্লাস্টিকের বোতাম। গর্ত যেখানে খোঁড়া হয়েছিল, তার ফুট দশেক দূরে। মৃতের শার্ট ছিঁড়ে গিয়ে ছিটকে পড়েছিল? খুনি বা খুনিদের সঙ্গে ধস্তাধস্তির সময়? বোতাম ছাড়াও সংগ্রহ করা হল ঘরের দেওয়ালে ছোপ ছোপ বাদামি দাগের স্যাম্পল। নিশ্চয়ই শুকিয়ে যাওয়া রক্ত?
সময় লাগল তল্লাশি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে। বিনোদ বর্মণের দেহ যখন বেরল মোমিনপুরের কাঁটাপুকুর মর্গের উদ্দেশে, রাত গড়িয়ে প্রায় সাড়ে এগারোটা। ইতিমধ্যে গোয়েন্দাপ্রধান এবং ডিসি সাউথ ঘুরে গেছেন অকুস্থল। ফোনে সব জানানো হয়েছে নগরপালকে। যিনি পত্রপাঠ কেসের তদন্তের ভার দিয়েছেন গোয়েন্দা বিভাগকে। রহস্যভেদের দায়িত্ব পেয়েছেন হোমিসাইড বিভাগের তৎকালীন সাব-ইনস্পেকটর সুশান্ত ধর (বর্তমানে গোয়েন্দা বিভাগেরই অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার হিসাবে কর্মরত), যিনি লালবাজার থেকে কালীঘাট আসার পথে সঙ্গী হয়েছিলেন ওসি হোমিসাইডের।
ময়নাতদন্ত হতে হতে পরের দিন দুপুর গড়িয়ে গেল। এই জাতীয় খুনের মামলায় অনেক ক্ষেত্রেই পোস্টমর্টেমের সময় তদন্তকারী অফিসার নিজেই উপস্থিত থাকেন। সুশান্তও ছিলেন। ময়নাতদন্ত জানাল, মাথায় কোনও ভারী জিনিসের আঘাতে খুন, ‘ante-mortem and homicidal’। এটুকু অনুমেয়ই ছিল। বাড়তি যেটা ডাক্তারবাবু বললেন, সেটাও মৃতদেহ আবিষ্কারের সময়ই আন্দাজ করা গিয়েছিল। এই খুনে ‘খুনি’ নয়, ‘খুনিরা’ যুক্ত। মৃত বিনোদের শারীরিক গঠন ছিল যথেষ্ট মজবুত। তাঁকে কাবু করে, নিশ্বাস বন্ধ করে মারার পর গর্ত খুঁড়ে পুঁতে দেওয়া, একার পক্ষে প্রায় অসম্ভবই।
কখন হয়েছিল খুনটা? দ্বিধাহীন জানালেন ডাক্তারবাবু, ২৫ তারিখ সকাল সাড়ে দশটা থেকে দুপুর দুটোর মধ্যে। দেহ উদ্ধার হয়েছিল ২৯ তারিখ বিকেলে। বিনোদকে খুন করা হয়েছিল তার প্রায় ৯৬ ঘণ্টা আগে!
খুনিদের সন্ধান শুরু করলেন সুশান্ত। বিকেল থেকে প্রায় মাঝরাত, কালীঘাট থানা এলাকায় ঘাঁটি গেড়ে পড়ে থাকলেন। বিনোদের পরিবারের লোকজন, স্থানীয় মানুষ এবং ওই অঞ্চলের পরিচিত সোর্সদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে যা তথ্য সংগ্রহ করলেন, সংক্ষেপে এরকম।
বর্মণ পরিবার আদতে বিহারের। কিন্তু প্রায় চার পুরুষ ধরে বসবাস কলকাতায়। কালীঘাটের ২, হিউম রোডের বাড়িতে। সোনারুপোর গয়নার পারিবারিক ব্যবসা ছিল বর্মণদের। বিনোদ বর্মণরা ছিলেন ছ’ভাই। বিনোদ সবার বড়। ব্যবসার দেখাশোনার পাশাপাশি কাজ করতেন ব্রিটানিয়া কোম্পানিতে। ২০০৩ সালে চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর পুরোপুরি মনোনিবেশ করেছিলেন ব্যবসায়।
মেজোভাই দিলীপ মারা গেছেন। সেজো ঘনশ্যাম তিরিশ বছর আগে বিবাগী হয়ে নিরুদ্দেশ। চতুর্থ ভাই অশোকের ব্যবসায়িক বুদ্ধির কিছু অভাব ছিল। স্বতন্ত্র দায়িত্ব নিতে গিয়ে প্রচুর টাকা লোকসান করেছিলেন। বিনোদকে সাহায্য করতেন ব্যবসার টুকিটাকি কাজে। কিন্তু ইদানীং সেটুকুও করতে পারতেন না ঘনঘন অসুস্থ হয়ে পড়ায়। পঞ্চম ভাইয়ের নাম প্রদীপ। ব্যবসার কাজে যে শ্রম এবং মনোযোগ প্রয়োজন, দুটোর কোনওটাই আয়ত্ত করে উঠতে পারেননি প্রদীপ। হাল ছেড়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত দিন গুজরান বাস্তুহারা বাজারে মাছ কেটে। ছোটভাই স্বপন জন্ম থেকেই বিকলাঙ্গ।
অসুস্থ বৃদ্ধা মা গোদাবরী দেবী মারা গিয়েছিলেন এই মাসের শুরুতেই। মা এবং বিকলাঙ্গ ছোটভাই স্বপনের চিকিৎসার সমস্ত খরচ বহন করতেন বিনোদই। ভাইদের মধ্যে আর্থিক সচ্ছলতা শুধু তাঁরই ছিল। প্রদীপ-অশোকের সংসারেও টানাটানি হত যখন, বড়দা বিনোদই ছিলেন সহায়।
বিনোদের স্ত্রী বেশ কয়েক বছর যাবৎ মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত। চিকিৎসা চললেও উন্নতি হয়নি বিশেষ। একমাত্র পুত্র রাজেশ ব্যবসার হাল ধরুন, আপ্রাণ চেয়েছিলেন বিনোদ। সে চাওয়া পূর্ণ হয়নি। ব্যবসার কাজে নিয়মিত সময় দেওয়ায় তীব্র অনীহা ছিল রাজেশের। বরং প্রবল উৎসাহ ছিল ব্যবসার টাকা মদ-মাংস-মোচ্ছবে উৎসর্গ করায়। শেষমেশ সমস্ত ব্যবসায়িক দায়দায়িত্ব থেকে বাধ্য হয়েই রাজেশকে অব্যাহতি দেন বিনোদ। মাসে মাসে রাজেশের জন্য নামমাত্র হাতখরচ বরাদ্দ করেছিলেন। অগত্যা রাজেশ শুরু করেন অটো চালানো। বিয়ে করেছেন বছরদুয়েক আগে। এখনও নিঃসন্তান।
বিনোদের বন্ধুমহলে কারা ছিলেন? দুটো নাম পেলেন সুশান্ত, যাদের সঙ্গে বিনোদের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। মন্টু দাস এবং প্রবাল দস্তিদার। দু’জনেই বিনোদের সমবয়সি, বয়স ষাট ছুঁইছুঁই। দু’জনেই কালীঘাটে বিনোদের পাড়ারই বাসিন্দা বহু বছর ধরে।
মন্টুবাবু পটুয়াপাড়ায় মূর্তি গড়ার কাজ করেন। কালীঘাটে মায়ের মন্দিরে প্রায় নিত্য যাতায়াত। প্রবালের কালীঘাট মার্কেটে একটা জামাকাপড়ের দোকান আছে ছোট।
মন্টু-প্রবালের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে একটা তথ্য পাওয়া গেল। বিনোদের নারীবিষয়ে স্বাভাবিকের বেশিই দুর্বলতা ছিল। স্ত্রী মানসিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে যে দুর্বলতা বেড়েছিল উত্তরোত্তর। নিষিদ্ধ পল্লিতে যাতায়াত ছিল নিয়মিত। দুই আবাল্য বন্ধুর কাছে কিছুই অজানা ছিল না।
ঈশ্বর গাঙ্গুলি স্ট্রিটে যে বাড়িটা বিনোদ বছরের শুরুতে কিনেছিলেন, তার লাগোয়া বাড়িতে বাস রীতা নস্কর নামের এক বছর চল্লিশের মহিলার। যাঁর স্বামী মারা গেছেন বছর পাঁচেক হল। এক ছেলে, হস্টেলে থেকে পড়াশুনো করে, ক্লাস নাইনে। এই রীতার সঙ্গে বিনোদের সম্পর্ক নিয়ে পাড়ায় নাকি কানাঘুষো হচ্ছিল ইদানীং। বিনোদ-রীতাকে নাকি একসঙ্গে স্থানীয় সিনেমাহলে দেখা গিয়েছিল বেশ কয়েকবার, এমন কথাও রটেছিল পাড়ায়।
রীতাকে সেদিন জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারলেন না সুশান্ত। ছেলের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন হস্টেলে। পরের দিন সকালের ট্রেনে কলকাতায় ফেরার কথা।
.
১ অক্টোবর, সকাল এগারোটা। লালবাজার।
অফিসে এসেই সোজা ওসি হোমিসাইডের ঘরে ঢোকেন সুশান্ত। তদন্তে এখনও পর্যন্ত যা যা তথ্য এসেছে হাতে, জানাবেন। আলোচনাও প্রয়োজন, কী কী ভাবে এগোনো যায়, সে নিয়ে।
—স্যার, পরিচিত লোকজন হওয়ারই সম্ভাবনা বেশি। বিনোদ যে রোজ সকালে ওই সময় ঈশ্বর গাঙ্গুলি স্ট্রিটের বাড়িতে যেতেন, জানত খুনিরা।
—হুঁ, অ্যাপারেন্টলি তাই মনে হচ্ছে। একেবারে অচেনা-অজানা কেউ দিনের বেলায় এসে ঘরে ঢুকে মেরে পুঁতে দিয়ে যাবে, এটা হাইলি আনলাইকলি। আচ্ছা, ও রাস্তায় তো মোটামুটি মানুষজনের ভিড় লেগেই থাকে। কেউ কিছু দেখেনি? আই মিন, কাউকে ঢুকতে ও-বাড়িতে?
—দেখার তো কথা। তবে খোঁজখবর করার সময়ও তো বিশেষ পাইনি। গতকাল বিকেল থেকে রাত তো বেসিক ইনফর্মেশন নিতেই কেটে গেল।
—সোর্স?
—লাগিয়েছি স্যার। কাল-পরশুর মধ্যে কিছু না কিছু খবর আসবেই।
—আচ্ছা, ধরেই নেওয়া যাক, পরিচিতরা মেরেছে। কারা হতে পারে, ভেবেছ কিছু? মানে, প্রিলিমিনারি আইডিয়া কোনও?
—দেখুন স্যার, একদিনে তো সবটা জানা হয়ে ওঠেনি। পরিচিতির বৃত্তে কারা কারা ছিলেন, ব্যবসায়িক শত্রুতা কিছু ছিল কিনা, সেসব ডিটেলে জানতে আরও দিনদুয়েক তো লাগবেই। তবে যাঁদের কথা এখন পর্যন্ত জানা গেছে, তাঁরা কেউই সন্দেহের বাইরে নয়। মোটিভ সকলেরই ছিল অল্পবিস্তর।
—যেমন?
—ধরুন স্যার, রাজেশ। ব্যবসা থেকে একরকম তাড়িয়েই দিয়েছিল বাবা। অটো চালিয়ে আর ক’পয়সা হয়? নেশার ঠেকে প্রায়ই দেখা যায়, সোর্স ইনফর্মেশন। টাকার দরকার ছিল। মোটিভ? বাবাকে মেরে ব্যবসার দখল নেওয়া। মিসিং ডায়েরিটা স্রেফ আমাদের মিসলিড করতে। আর ওই আকুলিবিকুলি কান্নাটা স্রেফ নাটক।
—হুঁ…
—আবার একই কারণে দুই ভাই অশোক আর প্রদীপকেও সন্দেহের তালিকার বাইরে রাখা যায় না। ওদের আর্থিক অবস্থাও ভাল ছিল না। তার উপর দাদার এই রমরমা।
—হ্যাঁ, কিন্তু যদি উইল-টুইল বিনোদ না করে গিয়ে থাকেন, লেখাপড়া যদি কিছু না থাকে, বিনোদের মৃত্যুর পর তো ব্যবসার দখল নিয়ে রাজেশ আর ওর কাকাদের মধ্যে ঝামেলা লাগবে।
—আমি এই পয়েন্টেই আসছিলাম স্যার। এমন হওয়াও অস্বাভাবিক নয় যে রাজেশ আর তার দুই কাকা মিলেই বিনোদকে মেরেছে। আফটার অল, কাজটা কারও একার নয়। খুনটা যে একাধিক লোক মিলে করেছে, সেটা তো পরিষ্কার।
—হুঁ, অসম্ভব নয়। আর রীতা? বা বন্ধু যে দু’জনের কথা বললে, মন্টু, আর কী যেন নাম অন্যজনের?
—প্রবাল। দুই বন্ধু মিলেও করতেই পারে। কিন্তু মোটিভ তো কিছু দেখছি না। ছোটবেলার বন্ধুকে মারতে যাবে কেন হঠাৎ? আর রীতা নস্করের সঙ্গে তো এখনও কথাই বলা গেল না। আজ বলব।
—হ্যাঁ, শুধু রীতা নন, সকলের সঙ্গেই আর একবার ডিটেলে কথা বলো আজ, সময় নিয়ে। থানাতেই ডেকে নাও বিকেলের দিকে।
—রাইট স্যার।
—আর হ্যাঁ, রাজেশ এবং অন্য যাঁদের কথা বললে, মোবাইল রেকর্ডস পেয়েছ? ভিক্টিমেরটা?
—রিকুইজিশন কাল সন্ধেবেলায়ই পাঠিয়ে দিয়েছি। শেষ তিন মাসের চেয়েছি। আজ সন্ধের মধ্যে ডেফিনিটলি পেয়ে যাব।
—হ্যাঁ, ওটা থেকে ‘লিড’ কিছু একটা পাওয়া উচিত। আর না পেলেও কয়েকজনকে ‘এলিমিনেট’ অন্তত করতে পারবে সাসপেক্টদের লিস্ট থেকে।
.
১ অক্টোবর, কালীঘাট থানা। বিকেল সাড়ে চারটে।
থানায় উপস্থিত বর্মণ পরিবারের তিন সদস্য রাজেশ-অশোক-প্রদীপ, দুই বাল্যবন্ধু মন্টু দাস-প্রবাল দস্তিদার, এবং প্রতিবেশিনী রীতা নস্কর। সুশান্ত থানায় চলে এসেছেন সোয়া চারটেয়। এঁদের প্রত্যেকের ব্যাকগ্রাউন্ডের ব্যাপারে আরও অনেক খোঁজখবর নেওয়ার আছে। প্রত্যেকের গতিবিধির উপর নজর রাখাও প্রয়োজন। সেসব করাই যাবে। মোবাইল রেকর্ডস এসে যাবে সন্ধের মধ্যে। কোনও অসংগতি পেলে চেপে ধরতে আর কতক্ষণ? এক রীতা ছাড়া প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ এঁদের সবারই হয়ে গেছে। তবু আরও একবার বাজিয়ে নেওয়া দরকার সবাইকে। এবং এই ‘বাজিয়ে নেওয়া’-র কাজটা একটু অন্যভাবে করবেন, ঠিক করলেন সুশান্ত। শুরু হল দ্বিতীয় দফার জেরা।
জেরা নিয়ে কিছু কথা প্রাসঙ্গিক এখানে। বাস্তবের তদন্তের অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে, তাঁদের যে কাউকে জিজ্ঞেস করে দেখবেন, জেরা বা জিজ্ঞাসাবাদ হল পৃথিবীর নীরসতম কাজগুলোর একটা। অন্তত তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে তো বটেই। শুরুর দিকে সন্দেহের পরিধি থাকে বিস্তৃত। নাম কী, বাবার নাম কী, বাড়ি কোথায়, কে কে আছে বাড়িতে, কী করেন, আগে কী করতেন… এমন গুচ্ছের কেজো প্রশ্নের মাধ্যমে সংগ্রহ তৈরি করতে হয় তথ্যভাণ্ডার। নীরস, কিন্তু জরুরি। ওটাই ভিত, ওটাই বুনিয়াদ। যার উপর বাড়ি উঠবে।
জেরার পদ্ধতি বা ‘Interrogation techniques’ নিয়ে প্রচুর তত্ত্ব আছে অপরাধবিজ্ঞানে। ১৯৭৪ সালে John E. Reid প্রবর্তিত ‘Reid Technique’ একসময় প্রবল সমাদৃত ছিল তদন্তকারীদের কাছে। বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। Reid-এর তত্ত্বের নির্যাস হল, জেরায় যত বেশি সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করো। তারপর অপরাধের ধরন এবং সন্দেহভাজনদের সঙ্গে সেই তথ্যের যোগসূত্র স্থাপন করো জিজ্ঞাসাবাদে।
কীভাবে? প্রত্যেক সন্দেহভাজনের জীবনধারা এবং চরিত্রবৈশিষ্ট্যের একটা ছবি এঁকে ফেলো মনে মনে। অমুকের আর্থ-সামাজিক অবস্থা কেমন, পারিবারিক জীবনই বা কেমন, কর্মজীবনে কতটা অস্থিরতা, প্রাথমিক প্রশ্নোত্তরে শরীরী ভাষায় কোনও উদ্বেগ ধরা পড়েছে কিনা, চিন্তিত হয়ে পড়লে কোনও মুদ্রাদোষ চোখে পড়ে কিনা, সব মগজে ‘স্টোর’ করে রাখো। সামগ্রিক ভাবে একটা নির্দিষ্ট ধারণা তৈরি করো, যাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, তার ব্যাপারে। সেই ধারণার ভিত্তিতে পরের পর্যায়ে প্রশ্নমালার গতিপথ নির্ধারণ করো। সে প্রশ্ন কখনও হোক আন্তরিক এবং তথ্যমূলক, কখনও ব্যক্তিবিশেষে হোক প্ররোচনামূলক। প্রতিক্রিয়া লক্ষ করো গভীর মনোযোগে এবং অপেক্ষায় থাকো উত্তরের অসংগতির। পরিভাষায়, ‘factual analysis’ আর ‘behaviour analysis’।
Reid-এর তত্ত্ব নিয়ে বিতর্কও আছে। পালটা তত্ত্ব আছে। অনেকে মনে করেন, এ ভাবে অপরাধীর থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের পদ্ধতি ‘থিয়োরি’ হিসাবে শুনতে ভাল। তবে বাস্তবে কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ আছে। সংশয় আছে ব্যবহারের বা শরীরী ভাষার তারতম্যের ভিত্তিতে ধারণা তৈরির বিষয়ে। পুলিশের প্রশ্নের মুখে পড়ে সম্পূর্ণ নিরপরাধ মানুষও নার্ভাস হয়ে যেতেই পারেন। হাতের তালু ঘেমে উঠতে পারে। পাল্স রেট বেড়ে যেতে পারে। অস্বাভাবিক কিছু নয়। আকছার হয়ে থাকে, দেখেছি আমরা। জেরার সময় ব্যবহারের পরিবর্তনের উপর মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপের পক্ষপাতী নন Reid Technique-এর বিরোধীরা। Reid-এর পদ্ধতিতে তত্ত্বের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য নিয়ে বরাবর আপত্তি জানিয়ে এসেছেন অপরাধবিজ্ঞানীদের একটা বড় অংশ।
আপত্তিটা কিন্তু উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা বলে, জিজ্ঞাসাবাদকে তত্ত্বের ঘেরাটোপে বন্দি করে ফেললে ফল মেলে না অনেক ক্ষেত্রেই। কোন ক্ষেত্রে কোন স্ট্র্যাটেজি কাজ করবে, বলা মুশকিল। জেরা করতে করতেই অনেক ক্ষেত্রে তদন্তকারীকে পদ্ধতি বদলে ফেলতে হয় পরিস্থিতির বিচারে। ব্যাকরণসিদ্ধ প্রথার পরোয়া করলে চলে না তখন।
যেমন ধরুন, বহুপ্রচলিত ‘Good cop, Bad cop’ টেকনিক। সন্দেহভাজনকে যদি কিছুটা আবেগপ্রবণ মনে হয়, এই পদ্ধতিতে কাজ হয় বেশি। ‘Bad cop’ অর্থাৎ ‘খারাপ পুলিশ’ ইচ্ছাকৃত ভাবে রূঢ় ভাষায় জেরা করে সন্দেহভাজনকে মানসিক ভাবে দুমড়ে দিলেন। আর কিছুক্ষণের বিরতির পর ‘Good cop’ অর্থাৎ ‘ভাল পুলিশ’ এসে পিঠে সহানুভূতির হাত রাখলেন, ‘আগের জনের কথায় কিছু মনে করবেন না প্লিজ়। নিন, জল খান। আপনি কী অসহনীয় পরিস্থিতিতে ক্রাইমটা করতে বাধ্য হয়েছেন, আমি বুঝি। আপনার জায়গায় থাকলে আমিও একই জিনিস করতাম। কিছু বলতে হবে না এখন আপনাকে। যখন ইচ্ছে হয়, বলবেন। না ইচ্ছে হলে বলবেন না।’
এই পন্থায় অভাবিত কাজ দেয় কখনও কখনও। বাবা খুব বকাবকি করার পর মা পিঠে হাত রেখে আদর করে দিলে, বা উলটোটা হলে, বাচ্চারা যেমন হাউহাউ করে কেঁদে ফেলে কাঙ্ক্ষিত সহানুভূতির ছোঁয়ায়, এ অনেকটা তেমন। ‘Good cop’-এর কাছে স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকারোক্তি আসে অপরাধের।
উদাহরণ আরও অনেক দেওয়া যায়। মোদ্দা কথা হল, তত্ত্বসর্বস্বতায় আটকে থাকতে নেই তদন্তকারীকে। টেকনিকের জন্য খেলা নয়। খেলার জন্যই টেকনিক। যে টেকনিকে যখন যেভাবে রান আসতে পারে, সেটাই তখন সেখানে ব্যাটসম্যানের সেরা টেকনিক। সে ব্যাটিং-ম্যানুয়াল যা-ই বলুক না কেন।
সুশান্ত জেরা শুরু করলেন ব্যাকরণের তোয়াক্কা না করেই। প্রথম থেকেই চালু করে দিলেন ‘শক থেরাপি’। মনস্তাত্ত্বিক ‘শক’, আচমকা ঝটকা। কথা নেই বার্তা নেই, শুরুতেই সবাইকে সরাসরি কাঠগড়ায় তোলা হতভম্ব-হতচকিত করে দিয়ে। এবং যাচাই করে নেওয়া বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের প্রতিক্রিয়া।
বাড়ি ফেরার কিছুটা তাড়াও ছিল সুশান্তর। সন্ধে হয়ে যাবে একটু পরেই। বৃষ্টি শুরু হয়েছে আকাশ ভেঙে। থামার ন্যূনতম লক্ষণ নেই। রাত্রে যাদবপুরে এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের ছেলের জন্মদিনের অনুষ্ঠান। একবার না গেলেই নয়। বুড়ি ছুঁয়ে আসাই, তবু একবার মুখ দেখাতেই হবে, সে যত রাতই হোক। এমনিতেই পুলিশ মহলে একটা রসিকতা চালু আছে, ‘পুলিশের শনিবার নেই, রবিবার নেই, পরিবার নেই।’ আজকের নেমন্তন্নটায় না গেলে সত্যিই ‘পরিবার’ থাকার সম্ভাবনা কম। বাড়িতে সবাই অপেক্ষা করে আছে, সুশান্ত ফিরলে একসঙ্গে যাওয়া হবে। কিন্তু এ যা বৃষ্টি শুরু হয়েছে, সময়মতো বেরতে পারলে হয়। বিরক্ত লাগে সুশান্তর, দ্রুত শুরু করেন রাজেশকে দিয়ে।
—ভাই, আপনি কিন্তু আগাগোড়া একটা কথা মিথ্যে বলেছেন।
হকচকিয়ে যান রাজেশ।
—আমি? কী স্যার?
—একটা ম্যাটাডোর কেনার টাকা চেয়েছিলেন বাবার কাছে। বিনোদবাবু দেননি। বলেছিলেন, ‘তোকে টাকা দেওয়া মানে জলে দেওয়া। মদ খেয়ে উড়িয়ে দিবি দু’দিনে।’ চেতলার জুয়ার ঠেকে এ নিয়ে তো পরদিন বাবাকে প্রচুর গালমন্দ করেছিলেন। বলেছিলেন, ‘দেখে নেব বুড়োকে!’
—ভুল খবর স্যার, ডাহা মিথ্যে!
—মোটেই মিথ্যে নয়! আপনি যান না চেতলা লক গেটের পাশের ঠেকে প্রতি রাত্রে?
রাজেশ আমতা আমতা করতে থাকেন এবার।
—যাই স্যার। অনেকেই যায়। কিন্তু বিশ্বাস করুন, বাবার কাছে টাকাও চাইনি আর ওসব বলিওনি ঠেকে। আপনি খোঁজ নিয়ে দেখুন স্যার।
—খোঁজ না নিয়ে কী আর বলছি? বাবাকে মেরে বাড়িটা হাতানোর মতলব করেছিলেন কিছু গুন্ডা-বদমাইশদের নিয়ে। ভুল বলছি?
রাজেশ রেগে যান হঠাৎ।
—হ্যাঁ স্যার, ভুল বলছেন। একশোবার ভুল বলছেন। হাজারবার ভুল বলছেন। আমি মরে গেলেও নিজের বাবাকে খুন করার কথা ভাবতেই পারব না। কী প্রমাণ আছে আপনাদের কাছে? যা খুশি বলে যাবেন, আর মেনে নিতে হবে?
সুশান্ত শোনেন চুপচাপ। সত্যিই, প্রমাণ তো কিছু নেই। এ তো স্রেফ আন্দাজে ঢিল ছোড়া চলছে। লাগলে তুক, না লাগলে তাক। মুখে অবশ্য বুঝতে দেন না রাজেশকে।
—কী প্রমাণ আছে, ঠিক সময়ে বলব। আমরা তো আর ঘাসে মুখ দিয়ে চলি না। কাল দুপুরের দিকে খবর পাঠাব। লালবাজারে চলে আসবেন।
রাজেশের চোখে আতঙ্কের ছায়া পড়ে।
—লালবাজারে কেন স্যার?
সুশান্ত থেমে থেমে উত্তরটা দেন, সময় নিয়ে।
—আসলে কী জানেন, থানায় বসে ঠিক হয় না। দেখছেন তো, কত লোক কত সমস্যা নিয়ে আসছে যাচ্ছে। এখানে ঠিক হয় না ব্যাপারটা। লালবাজারে আলাদা ঘর আছে জেরা করার। কাল আসুন, বুঝতে পারবেন। নিশ্চিন্ত থাকুন, যত্নআত্তির কোনও ত্রুটি হবে না।
রাজেশের আতঙ্ক দৃশ্যতই আরও গাঢ় হয়। লালবাজারে যত্নআত্তি মানে? পাশে বসে থাকা মন্টুবাবুর হাত চেপে ধরেন রাজেশ।
—মন্টুকাকু, স্যাররা ভাবছেন আমি বাবাকে মেরেছি। আমি কেন নিজের বাবাকে মারতে যাব? তুমি তো আমাকে ছোট থেকে দেখেছ। তোমার মনে হয়, আমি বাবাকে মারতে পারি? তুমি বলো স্যারকে …
মন্টু সত্যিই রাজেশকে জন্মাতে দেখেছেন, বিনোদের সঙ্গে প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছরের অভিন্নহৃদয় বন্ধুত্ব। পিঠে হাত রাখেন পুত্রসম রাজেশের, তাকান সুশান্তর দিকে।
—স্যার, জানি না কী প্রমাণ পেয়েছেন আপনারা। তবে এটুকু বলতে পারি, আর যাই করুক, খুন করার ছেলে রাজেশ নয়। বিশ্বাস করুন।
সুশান্ত সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন মন্টুকে। তাকান রীতার দিকে।
—কিছু মনে করবেন না রীতাদেবী, আপনার সঙ্গে বিনোদবাবুর সম্পর্ক ঠিক কেমন ছিল?
মহিলা এ প্রশ্ন আশা করেননি। অবাক দৃষ্টিতে তাকান।
—কেমন সম্পর্ক মানে?
—মানে আর নতুন করে কী বোঝাব? আপনিও বুঝছেন, কী বলতে চাইছি। বিনোদবাবুর সঙ্গে আপনার অবৈধ সম্পর্কের কথা বলছি। বাধ্য হয়েই বলছি।
—এসব কী বলছেন স্যার!
—আপনার অজানা কিছু বলছি কি? আর না জেনে এ ধরনের কথা বলবই বা কেন? বিনোদ যখন ঈশ্বর গাঙ্গুলির বাড়িতে যেতেন রোজ, মাঝেমাঝে আপনি যেতেন না দুপুরের দিকে? কেন যেতেন? ওঁর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বাড়িটা নিজের নামে লিখিয়ে নিতে জোর করতেন না? একটা শব্দও মিথ্যে এর?
রীতা কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন সুশান্তর দিকে। তারপর কেঁদেই ফেলেন প্রায়।
—এ আপনি কী বলছেন স্যার? বিনোদদার সঙ্গে দাদা-বোনের সম্পর্ক ছিল। ওঁর বাড়িতে যাইই নি কোনওদিন। উনিই বরং গত ভাইফোঁটায় আমার বাড়িতে এসে ফোঁটা নিয়ে গেছেন। রাস্তাঘাটে দেখা হলে দু’-একটা কথা হত। আলাপ ছিল। এইটুকুই। খোঁজ নিয়ে দেখুন না পাড়ায়, সেলাই করে সংসার চালাই। মিথ্যে স্যার, আপনাকে যে এসব খবর দিয়েছে, মিথ্যে বলেছে। ডাকুন না একবার আমার সামনে…
—সময় হলেই ডাকব। যাক গে, বৃষ্টি থামলে বাড়ি যেতে পারেন। আরও কিছু জিজ্ঞেস করার আছে। কাল বিকেলের দিকে আপনাকেও একবার লালবাজার আসতে হতে পারে। থানা জানিয়ে দেবে, কখন।
রীতার মুখ থেকে কথা বেরয় না। চেয়ারেই বসে থাকেন। যেন নড়াচড়ারও ক্ষমতা হারিয়েছেন।
সুশান্ত দেখেও দেখেন না। ঘড়িতে চোখ বুলোন। পৌনে ছ’টা। দেরি হয়ে যাচ্ছে। মন্টু-প্রবাল-অশোক-প্রদীপ এখনও বাকি। তাড়াতাড়ি সেরে বেরতে হবে এবার। বৃষ্টিটা ধরে এসেছে একটু। থামেনি, তবে আগের মতো মুষলধার চোখরাঙানি নেই।
—মন্টুবাবু, কী কী কারণে আপনি বাল্যবন্ধু বিনোদকে খুন করতে পারেন বলবেন একটু…
কথা জোগায় না স্তম্ভিত প্রৌঢ়র মুখে। সুশান্ত আবার জিজ্ঞেস করেন।
—বলুন মন্টুবাবু… কেন মারলেন বিনোদবাবুকে? ছোটবেলার বন্ধুকে এভাবে মারতে হাত কাঁপল না? আপনার তো নরকে ঠাঁই হওয়াও মুশকিল …
মন্টুকে আক্ষরিক অর্থেই বাক্রুদ্ধ দেখায়।
—স্যার, আমি ছাপোষা মানুষ। কালীঘাট মন্দিরে পাঁঠাবলি দিই, পটুয়াপাড়ায় মূর্তি বানাই। গায়ক অমৃক সিং অরোরার নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন স্যার? ওঁর বাড়ির কালীপুজোয় আমিই মূর্তি বানাই বহু বছর হল। জিজ্ঞেস করে দেখবেন আমার ব্যাপারে। আমি খুন করব বিনোদকে?
—সে না হয় জিজ্ঞেস করব। আর আপনি যদি না-ও মেরে থাকেন, আর কে মারতে পারে আপনার বন্ধুকে? কী মনে হয়?
বিহ্বল মন্টু হাতজোড় করে ফেলেন এবার। চশমা খুলে চোখ মোছেন।
—কী বলব স্যার? বিনোদের তো কোনও শত্রু ছিল না। নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ ছিল।
সুশান্তর হঠাৎই চোখ চলে যায় করজোড় মন্টুর বাঁ হাতের দিকে। লাল ছোপ একটা বুড়ো আঙুলে।
ইনস্টিংক্ট। ইংরেজি শব্দ। কী বাংলা হয়? সহজাত প্রবৃত্তি? আগাথা ক্রিস্টির ‘The Mysterious Affair at Styles’ উপন্যাসে অদ্বিতীয় Hercule Poirot এক জায়গায় বলছেন, ‘Instinct is a marvellous thing. It can neither be explained, nor can be ignored.’ সহজাত প্রবৃত্তি এক আশ্চর্য বস্তু। ব্যাখ্যাও করা যায় না, উপেক্ষাও না।
জিজ্ঞাসাবাদের সময় সন্দেহভাজনের শরীরের প্রতিটি নড়াচড়া শ্যেনদৃষ্টিতে লক্ষ করা যে-কোনও বুদ্ধিমান তদন্তকারীর সহজাত প্রবৃত্তি, স্বাভাবিক ইনস্টিংক্ট। যেটা অভাবিত ভাবে কাজে লেগে গেল সুশান্তর।
—ওটা কীসের দাগ মন্টুবাবু? লাল দাগটা?
মন্টুকে সামান্য অপ্রস্তুত দেখায়, সামলে নেন পরমুহূর্তেই।
—মূর্তি গড়ি তো, রং লেগে যায়, লেগে গেছে অসাবধানে।
সুশান্ত উঠলেন চেয়ার ছেড়ে। মন্টুবাবুর বাঁ হাতটা ধরে লাল ছোপটা দেখলেন মিনিটখানেক। স্থির দৃষ্টিতে তাকালেন চোখাচোখি।
—মিথ্যে বলছেন কেন? এটা মূর্তির রং নয়। এটা তো লাল ওষুধ, মারকিউরোক্রোম।
মন্টুবাবু ফ্যালফ্যাল করে তাকান সুশান্তর দিকে। তোতলাতে থাকেন হঠাৎ।
—পাঁঠা কাটি তো… রক্ত ছিটকে বোধহয়…
সুশান্ত শোনেন, এবং আগ্রাসী আক্রমণে যান নিমেষে। লোভনীয় ফ্লাইটেড ডেলিভারিতে ঠিক যেভাবে স্টেপ আউট করে ব্যাটসম্যান।
—একবার বলছেন মূর্তির রং, একবার বলছেন বলির রক্ত। আমাকে দেখে যদি নির্বোধ বলে মনে হয় আপনার, তা হলে ভুল মনে হয়। কোথায় কেটে গেছে আপনার? লাল ওষুধের দরকার পড়ল কেন?
মন্টু বসে থাকেন বজ্রাহতের মতো। টেনে দাঁড় করান সুশান্ত।
—জামাটা খুলুন।
জামা খোলার পর দেখা গেল, মন্টুর ডান কনুইয়ের কাছে ছড়ে যাওয়ার চিহ্ন। দেখেই বোঝা যায়, ক্ষত খুব পুরনো নয়। সবে মামড়ি পড়তে শুরু করেছে। ফরেনসিক সায়েন্সের ভাষায়, ‘brush abrasion’, রাফ সারফেসের সঙ্গে শরীরের কোনও অংশের ঘর্ষণজনিত ক্ষতচিহ্ন।
—এটা কবে হল? কী ভাবে হল?
মন্টু নিরুত্তর। কাঁপছেন। সুশান্ত বলতে থাকেন।
—আমি বলি? আমি বলি, কীভাবে হয়েছিল? বিনোদকে খুন করে যখন বডিটা টেনেহেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন পোঁতার জন্য, দেওয়ালে ঘষা লেগেছিল। ঠিক বলছি?
স্রেফ আন্দাজেই বলা, এবং লক্ষ্যভেদ! মন্টু দাস কাঁপতে কাঁপতে চেয়ার ছেড়ে মাটিতে বসে পড়েন। পা জড়িয়ে ধরেন সুশান্তর। কাঁদতে শুরু করেন অঝোরে।
—সব বলছি স্যার। আমি একা মারিনি। অশোক আর প্রদীপও ছিল।
অশোক বর্মণ আর প্রদীপ বর্মণ, মৃত বিনোদের দুই সহোদরের দিকে তাকান সুশান্ত। দু’জনে যেন সহসাই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট। বেঞ্চে চুপচাপ বসে থাকা রাজেশ শুনছিলেন সব। আচমকা উঠে দাঁড়িয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন অশোকের উপর, ঝাঁকাতে থাকেন কাকার শার্টের কলার, ‘তোমরা মেরেছ বাবাকে? তোমরা?’
দু’জন কনস্টেবল সরিয়ে নিয়ে যান রাজেশকে। মোবাইল কল রেকর্ডের আর দরকার পড়বে না আপাতত, বোঝেন সুশান্ত। বোঝেন, ওসি হোমিসাইডকে ফোন করা দরকার এখনই। বোঝেন, নেমন্তন্ন রক্ষা লাটে উঠল। বাড়ি যাওয়ার কোনও গল্পই নেই আর। ‘পরিবার’ থাকবে কিনা, ভাবার সময় নেই এখন।
মন্টু বলতে শুরু করলেন। মুখ খুললেন অশোক আর প্রদীপও। পরদা উঠল হত্যারহস্যের।
বিনোদদের মা গোদাবরী দেবী সেপ্টেম্বরের শুরুতে মারা যাওয়ার পরই মায়ের ঘরের দখলদারি নিয়ে অশোক-প্রদীপের সঙ্গে ঝামেলা শুরু হয় বিনোদের। মায়ের ঘরের সম্পূর্ণ দখল নিতে চেয়েছিলেন বিনোদ, একরকম জোর করেই। বাধা দেন অশোক-প্রদীপ। মায়ের শ্রাদ্ধের দিনও তীব্র বাদানুবাদ হয় এ নিয়ে। বিনোদ বলেন, ‘মায়ের চিকিৎসার সব খরচ যখন আমি দিতাম, ঘরের উপর আমারই দাবি সবার আগে।’ এ যুক্তি মানতে চাননি ভাইরা। যাঁরা নিজেদের দিন-আনি-দিন-খাই জীবনযাত্রার সঙ্গে বড়দার রাজা-মারি-বাদশা-মারি চালচলনের তুলনা করে দীর্ঘদিন যাবৎ ভুগতেন হীনম্মন্যতায়, ঈর্ষায়। যে ঈর্ষায় প্রবল ঘৃতাহুতি দিয়েছিল বিনোদের ঘর দখলের চেষ্টা।
মন্টু দাস এ পরিবারের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ। অশোক-প্রদীপদের বড় হতে দেখেছেন। মন্টুদা-র শরণাপন্ন হলেন দুই ভাই, ‘তুমি বড়দাকে বোঝাও। ওর টাকার জোর আছে। ঠিক কোনওভাবে ঘরটা দখল করে নেবে। জোরজার করলে কিন্তু আমরাও ছাড়ব না। টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করে বলে উঠতে-বসতে গালিগালাজ করে। কথা শোনায় রোজ। অনেক সহ্য করেছি। আর নয়। তা ছাড়া ঈশ্বর গাঙ্গুলি স্ট্রিটের বাড়িটাও তো আছে। ওটা বেচে দিলে তো অনেক টাকা পাবে। মায়ের ঘরটাও দরকার? বাড়াবাড়ি করলে খুনোখুনি হয়ে যাবে। মেরেই ফেলব।’
অশোক আর প্রদীপ জানতেন না, বিনোদের ব্যাপারে ঈর্ষা শুধু তাঁরাই নন, আপাতদৃষ্টিতে অভিন্নহৃদয়ের বন্ধু মন্টুও পোষণ করতেন।
—স্যার, একসঙ্গে বড় হয়েছি বিনোদের সঙ্গে। হাফপ্যান্টের বয়সের বন্ধু। গত এক-দেড় বছরে ব্যবসার যত রমরমা বাড়ছিল, বিনোদ যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করেছিল। আচার-আচরণই পালটে গেছিল। একসঙ্গে আড্ডা দিতাম বা তাস খেলতাম ঠিকই। কিন্তু ও মাঝেমাঝেই কথাবার্তায় বুঝিয়ে দিত, যে ও বড়লোক আর আমরা ছাপোষা। ও পেরেছে, আমরা পারিনি।
—বলে যান, শুনছি।
—আমারও স্যার টানাটানির সংসার। কোনওভাবে দিন চলে। পুজোর মরশুমেই যা মূর্তি গড়ে টাকা আসে কিছু। বাকি বছরটা চালাতে প্রাণ বেরিয়ে যায়।
—টানাটানির সংসার বলে ছোটবেলার বন্ধুকে মেরে ফেললেন? মেরে পুঁতে রাখলেন?
—বিশ্বাস করুন, বিনোদকে মারার কথা দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি কোনওদিন। গত মাসে ওর থেকে কিছু টাকা ধার চেয়েছিলাম বাড়িটা সারানোর জন্য। বেশি নয়, হাজার পাঁচেক। শুনে হাসতে হাসতে বলল, ‘দিতে পারি, কিন্তু শোধ দিবি, তার গ্যারান্টি কী? ফস করে কোনদিন মরে যাবি, আমার টাকা জলে যাবে।’ ওই অপমানটা প্রচণ্ড গায়ে লেগেছিল আমার। নিজেকে খুব ছোট মনে হয়েছিল। মুখে শুধু বলেছিলাম, ‘দিতে হবে না টাকা।’ বিনোদ তারপরেও দিতে চেয়েছিল টাকা। নিইনি। সম্মানে লেগেছিল। রাগ হয়েছিল খুব। দয়া দেখাচ্ছে?
—তারপর?
—অশোক-প্রদীপরা যখন এসে বলল, বিনোদ মায়ের ঘরের দখল নিতে চাইছে, যখন বলল, জবরদস্তি করলে ওরা মেরেই ফেলবে ‘বড়দা’-কে, আমার মাথায় একটা প্ল্যান এল। নিজের ভাইদের সঙ্গে যে কুকুর-ছাগলের মতো ব্যবহার করে, টাকার গরমে ছোটবেলার বন্ধুকে অপমান করতে যার বাধে না, তার চরম শাস্তিই পাওয়া উচিত।
—প্ল্যানটা কী করলেন?
—ঈশ্বর গাঙ্গুলি স্ট্রিটের বাড়িটা ভাল করে সারিয়ে-সুরিয়ে বেচে দেওয়ার কথা ভাবছিল বিনোদ। আমাকে বলেছিল, ‘দ্যাখ না একটা ভাল কোনও খদ্দের।’ আমি অশোক-প্রদীপকে বললাম, ‘তোদের বড়দা এই বাড়িটা বেচে দিয়ে মোটা টাকা পাবে আর সেই দিয়ে ব্যবসা আরও ফুলেফেঁপে উঠবে। মামলা করে তোদের মায়ের ঘরটাও দখল নেবে। একটা উপায় আছে আমাদের তিনজনেরই বড়লোক হওয়ার। শুনতে চাস তো বলব।’
অশোক এবার থামিয়ে দেন মন্টুকে।
—আমি বলছি স্যার। মন্টুদা বলল, ‘বিনোদের কাছ থেকে বাড়ির দলিলটা কোনওভাবে বাগিয়ে তারপর পৃথিবী থেকেই সরিয়ে দিতে পারলেই কেল্লা ফতে। দলিলটা জাল করে বাড়িটা বিক্রি করে যা টাকা পাব, সেটা তিনজন ভাগ করে নেব।’
প্রদীপ বলতে শুরু করেন অশোকের কথা শেষ হতে না হতেই।
—আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম মন্টুদাকে, ‘যদি পুলিশ ধরে ফেলে?’ মন্টুদা বলেছিল, ‘আরে, বডি পেলে তো ধরবে। পুঁতে দেব মাটির নীচে। খুঁজেই তো পাবে না কেউ। লোকে কিছুদিন পরে ভাববে, মেন্টাল পেশেন্ট বউ-কে ফেলে রেখে বাড়ি বেচে অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে চলে গেছে অন্য কোথাও। দ্যাখ ভেবে, তোরা রাজি আছিস কিনা?’
বক্তা এবার অশোক।
—বাড়ি ফেরার পথে আমরা দু’জন আলোচনা করে ঠিক করলাম, রোজকার অর্থকষ্ট আর বড়দার অপমানের থেকে বাঁচতে এটাই সেরা রাস্তা।
সুশান্ত ইশারায় থামতে বলেন দুই ভাইকে। তাকান মন্টুর দিকে। শক্ত সবল চেহারার প্রৌঢ় মাথা নিচু করে বসে আছেন নিশ্চুপ।
—মন্টুবাবু, বাকিটা আপনার মুখ থেকেই শুনি। ধরা তো পড়েই গেছেন, চুপ করে থেকে আর লাভ নেই।
উনষাট বছরের মন্টু মুখ তোলেন, বলতে থাকেন ধীরে ধীরে, বন্ধুহত্যার বৃত্তান্ত।
—২৪ তারিখ সন্ধেবেলা বিনোদকে ফোন করলাম। বললাম, ‘একজন ভাল খদ্দের পেয়েছি। বাড়িটা দেখতে চাইছে। দলিলটা নিয়ে কাল সাড়ে এগারোটায় আসতে পারবি?’ জানতাম, ওই সময়টায় রোজ ও এমনিতেই আসে। বিনোদ বলল, ‘ঠিক আছে, আসব।’
—আসার পর?
—রাতেই জানিয়ে দিয়েছিলাম অশোক-প্রদীপকে। কথা ছিল, ওরা কাছেপিঠে থাকবে। বিনোদ এলে আমি ঢুকব। ঢোকার আগে একটা মিসড কল দেব অশোককে। ওরাও চলে আসবে পাঁচ মিনিটের মধ্যে।
—বেশ …
—বিনোদ এল দলিল নিয়ে। আমি টুকটাক কথাবার্তা চালালাম কয়েক মিনিট। বিনোদ জানতে চাইল, ‘খদ্দের কখন আসবে রে?’ আমি বললাম, ‘এখুনি এসে পড়বে।’ বলতে বলতেই অশোক আর প্রদীপ ঢুকল। বিনোদ চমকে উঠে বলল, ‘আরে, তোরা?’
প্ল্যানমাফিক একটা বড় ব্যাগে শাবল আর কয়েক টুকরো কাপড় নিয়ে এসেছিল ওরা। বিনোদ কিছু বোঝার আগেই ব্যাগ থেকে শাবলটা বার করলাম আমি। ওরা দু’জন বিনোদের হাত চেপে ধরল, আর আমি সজোরে শাবল চালালাম কপালে। পরপর দু’বার। বিনোদ কাটা গাছের মতো পড়ে গেল।
—তারপর গলায় কাপড়ের ফাঁস দিলেন, মুখে কাপড় গুঁজলেন, আর বাড়ির পিছনে বিনোদকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে গিয়ে শাবল দিয়ে মাটি খুঁড়ে পুঁতে দিলেন, এই তো?
—হ্যাঁ স্যার, তার আগে বিনোদের প্যান্ট-জামা খুলে নিয়েছিলাম। প্যান্ট থেকে চাবির গোছাটা নিলাম। মেঝের রক্তের দাগ জল দিয়ে ভাল করে ধুয়ে ঘর তালাবন্ধ করে দলিলটা নিয়ে বেরিয়ে এলাম। বিনোদের শার্ট-প্যান্ট ব্যাগে ভরে নিয়ে।
.
প্রমাণ একত্রিত করার কাজটা খুব দুঃসাধ্য ছিল না চার্জশিট তৈরির সময়।
এক, রক্তের দাগ-লাগা শাবল উদ্ধার হয়েছিল অশোকের ঘর থেকে। রক্তের দাগের নমুনা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় মিলে গিয়েছিল ঘরের দেওয়াল থেকে সংগৃহীত রক্তের নমুনার সঙ্গে।
দুই, বিনোদের রক্তমাখা শার্টপ্যান্ট মন্টু দাসের বাড়ির তল্লাশিতে পাওয়া গেছিল। এক্ষেত্রেও পোশাকের রক্তের নমুনা আর অকুস্থল থেকে সংগৃহীত রক্তের নমুনা মিলে গিয়েছিল পরীক্ষায়। উদ্ধার হওয়া শার্টে একটা বোতাম ছিল অমিল। ঘটনাস্থল থেকে বাজেয়াপ্ত হওয়া প্লাস্টিকের বোতামই যে সেই বোতাম, একই শার্টের, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের রিপোর্টে নিখুঁত প্রমাণিত হয়েছিল।
তিন, প্রদীপের কাছে ছিল বিনোদের সেই বাড়ির দলিল। উদ্ধার হয়েছিল হিউম রোডের বাড়িতে প্রদীপের ঘরের ট্রাঙ্ক থেকে।
চার, কফিনে শেষ পেরেক ঠুকেছিল বিনোদ এবং আততায়ী-ত্রয়ীর কল রেকর্ড। খুনের আগের সন্ধেয় বিনোদকে ফোন মন্টুর, খুনের দিন সকালে মন্টুর মিসড কল অশোককে, চারজনের ফোনের টাওয়ার লোকেশন খুনের সময় একই বিন্দুতে মিলে যাওয়া, পারিপার্শ্বিক প্রমাণও ছিল অকাট্য।
পাঁচ বছরের বিচারপর্বের শেষে মন্টু-অশোক-প্রদীপকে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা শুনিয়েছিলেন বিচারক। কারাদণ্ড যাবজ্জীবন। যে সাজা ওঁরা এখনও ভোগ করছেন।
স্বামী-স্ত্রীকে খুন করছে সন্দেহের বশে। স্ত্রী ষড়যন্ত্রে শরিক হচ্ছে প্রেমিকের সঙ্গে, স্বামীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে। ছেলে সম্পত্তির লোভে ছক কষছে বাবার ভবলীলা সাঙ্গ করার। বাবার হাত কাঁপছে না সন্তান-নিধনে। ছোটবেলার বন্ধু অর্থলিপ্সায় পথের কাঁটা ভাবছে বন্ধুকে, বন্ধুর ভাইদের সঙ্গে সজ্ঞানে প্ল্যান করছে খুন করে মাটিতে পুঁতে দেওয়ার!
কল্পনার গল্প-উপন্যাসে এসব পড়া এক। বাস্তবের এমন ব্যতিক্রমী ঘটনা কাগজে পড়া এক। কিন্তু ঘটনায় জড়িত রক্তমাংসের চরিত্রগুলোর সঙ্গে তদন্ত চলাকালীন নিয়মিত ভাবের আদানপ্রদান আরেক। তদন্ত যাঁরা করেন এ ধরনের বিরল মামলায়, তাঁদের কিছুটা সুযোগ ঘটে অপরাধীর মনোজগৎকে সত্তর মিলিমিটার স্ক্রিনে দেখার।
দেখেও যে খুব বেশি শেখা যায়, এমন দাবিই বা করি কী করে? সম্পর্কের যোগ-ভাগ-গুণ-বিয়োগ মেলে না অপরাধের দুনিয়ায়। এ এক অন্য পৃথিবী।
বিপুলা যে পৃথিবী। যার কতটুকুই বা জানি!
পুনশ্চ: রীতা নস্কর নামটি পরিবর্তিত। মহিলার সামাজিক বিড়ম্বনা অভিপ্রেত নয়। তাই।
২.০৮ আংটি, তবে বাদশাহি নয়
[শ্যামপ্রসাদ রায় হত্যা
শুভজিৎ সেন, মেট্রো রেল পুলিশের ওসি।]
ওরা ছুটছে। পাশাপাশি, ঊর্ধ্বশ্বাসে। নিজের নিজের ট্র্যাকে। শুরুর দিকে পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান উনিশ-বিশ। কিন্তু সেটা ওই শুরুর দিকেই যা। তিরিশ-চল্লিশ মিটার পরেই ছবিটা বদলে যাচ্ছে দ্রুত। তিন-চারজনের একটা দল ছিটকে বেরিয়ে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। তাল রাখতে পারছে না বাকিরা।
ফিনিশিং পয়েন্টের একশো মিটার আগে একটা টার্ন আছে। তারপর এসপার-ওসপারের দৌড়। হাতে দূরবিন উঠে এসেছে জনতার। প্রতিটা ইঞ্চি-সেন্টিমিটারের এগোনো-পিছনোয় জান্তব উল্লাস ছিটকে আসছে গ্যালারি থেকে। উত্তেজিত ধারাভাষ্য যথেচ্ছ বারুদ জোগাচ্ছে সে উল্লাসে, ‘Number 3 in the lead, but for how long? 2 catching up fast, so is 5 and keep an eye on number 4 too.. Goodness me, this is as close as it gets!’
ওরা ছুটতে থাকে মরণ-বাঁচন। দৌড় শেষ হয়। আনন্দ-হতাশা-উচ্ছ্বাস-আক্ষেপের কোলাজ তৈরি হয় গ্যালারিতে। ফার্স্ট-সেকেন্ড-থার্ড, ফলাফল ঘোষণার পর ধারাভাষ্যকার রাশ টানেন নাটকীয়তায়, স্বাভাবিক গলায় জানিয়ে দেন পরের দৌড়ের সময়। অন্য ঘোড়া, অন্য দৌড়।
শুভজিৎ দেখছিলেন উদাসীন। রেসের মাঠে জীবনে আসেননি এই খুনটা হওয়ার আগে। আজ এই প্রথমবার এলেন। কে জানে, আর কতবার আসতে হবে? যখন ফোনটা থানায় এসেছিল সপ্তাহখানেক আগে, কে ভেবেছিল, এত ঝক্কি পোহাতে হবে? কে ভেবেছিল, এতটা সময় কাটাতে হবে ঘোড়দৌড়ের মাঠে?
.
১৬ অগস্ট, ২০০৭, বৃহস্পতিবার।
—নমস্কার, টালিগঞ্জ থানা…
স্বভাবসিদ্ধ কেজো গলায় ফোনটা তুলেছিলেন শুভজিৎ। থানায় ঢুকে নিজের চেয়ারে বসেছেন আধঘণ্টা হল। লম্বা দিন সামনে। একটু পরে আলিপুর কোর্টে যেতে হবে একটা পুরনো মামলায় সাক্ষী দিতে। একটা বধূনির্যাতন আর একটা চুরি, অন্তত দুটো মামলার চার্জশিট লিখে ফেলতেই হবে আজ। নানা ঝামেলায় লেখা হয়ে ওঠেনি। একটু বেশিই দেরি হয়ে গেছে। বড়বাবু গত রাতেও তাগাদা দিয়েছেন। বকাঝকাও করেছেন একটু।
চুরির কেসটার চার্জশিটে হাত দিতে না দিতেই ফোনের ক্রিং ক্রিং। একটু বিরক্তি নিয়েই রিসিভার কানে নিয়েছিলেন শুভজিৎ। এবং দূরভাষের অন্য প্রান্ত থেকে যা ভেসে এসেছিল, শুনে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়তে কয়েক সেকেন্ডই লেগেছিল মাত্র।
—স্যার, এখানে একটা মার্ডার হয়ে গেছে।
—এখানে মানে?
—পার্ক সাইড রোড, ২৪ নম্বর। তাড়াতাড়ি আসুন স্যার… খুন…
গাড়িতে থানা থেকে দূরত্ব খুব বেশি হলে মিনিট পাঁচেক। আর একটা কেস সম্ভবত ঘাড়ে চাপতে যাচ্ছে, যেতে যেতে ভাবছিলেন শুভজিৎ। সব মামলায় মগজের পুষ্টি হয় না। চুরি-ছিনতাই ইত্যাদির অধিকাংশই তো ‘ধর তক্তা মার পেরেক’ ঘরানার তদন্ত। আর খুনের মামলা মানেই যে রহস্য হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে, এমনও নয়।
দশের মধ্যে ন’টা মামলায় রোমাঞ্চ-অ্যাডভেঞ্চার-উত্তেজনা অনেক দূরের গ্রহ। বেশিরভাগ খুনের মামলায় প্রথম দিনই জানা হয়ে যাচ্ছে, খুনি কে। হয় গৃহভৃত্য মনিবকে খুন করে টাকাপয়সা লুঠ করে পলাতক, নয় পুরনো শত্রুতার জেরে বন্ধুকে খুন বন্ধুর। বা, প্রত্যাখ্যান সহ্য না করতে পেরে প্রেমিকাকে খুন প্রেমিকের। রহস্য কই? শুধু ফেরার অপরাধীকে গ্রেফতার, গুচ্ছের লোকের জবানবন্দি নেওয়া, চার্জশিটে যাতে ফাঁকফোকর না থাকে, সেটা দেখা। মাথা খাটানোর মতো মামলা বছরে বড়জোর একটা-দুটো। ওই বুদ্ধি খরচ করার প্রক্রিয়াটা দারুণ লাগে শুভজিতের। ওই জন্যই তো পুলিশের চাকরিতে আসা।
ছোটবেলা থেকে গোয়েন্দা গল্পের পোকা। ফেলুদা-ব্যোমকেশের মতো একটার পর এক রহস্যের সমাধান করবেন, এমনই ভাবতেন শুভজিৎ স্কুলবেলায়। চাকরিতে এসে সাময়িক মোহভঙ্গ ঘটেছিল, কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের আকাশপাতাল তফাতে। কোথায় ফেলুদার মগজাস্ত্রের রোম্যান্স, আর কোথায়ই-বা ব্যোমকেশ বক্সীর সত্যান্বেষণের রোমাঞ্চ! কল্পনার গোয়েন্দাকাহিনির গা-ছমছম উত্তেজনা যদি হয় সবুজে সবুজ ইডেন গার্ডেন্স, বাস্তবের তদন্ত তুলনায় ছিরিছাঁদহীন কাঁকরভরতি পাড়ার ফুটবল মাঠ।
ভাবনায় ছেদ পড়ে ড্রাইভারের ব্রেক কষার শব্দে। গাড়ি থেমেছে একটা জটলার সামান্য দূরে। পুলিশের গাড়ি দেখে কয়েকজনকে উৎসুক ভঙ্গিতে এগিয়ে আসতে দেখে শুভজিৎ বোঝেন, ‘স্পট’-এ পৌঁছে গেছেন।
রাসবিহারী মোড় থেকে যদি হাঁটা দেন গড়িয়াহাটের দিকে, কিছুটা এগিয়ে বাঁ হাতে পড়বে পার্ক সাইড রোড। ঢোকা যায় শরৎ বোস রোডের দিক থেকেও। রাস্তার দু’ধারের বাড়িগুলোর দিকে একবার চোখ বুলোলেই বোঝা যায়, এ মহল্লায় উচ্চবিত্তেরই বাস প্রধানত।
বছর তিরিশের এক যুবক এগিয়ে আসেন শুভজিতের দিকে।
—স্যার, থানায় আমিই ফোন করেছিলাম। কয়েকটা বাড়ি পরেই থাকি। বাজার করে ফিরছিলাম। ২৪ নম্বরের ফ্ল্যাটগুলোয় যে ছেলেটা সপ্তাহে দু’বার সিঁড়ি-টিঁড়ি ঝাঁট দিতে আসে, সেই প্রথম নেমে এসে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেছিল। গন্ধ পেয়ে ওর সন্দেহ হয়েছিল। ভয়ও পেয়েছিল। অনেকবার বেল বাজিয়েও সাড়া পায়নি ভিতর থেকে। আমরা কয়েকজন গেলাম। যা বিশ্রী গন্ধ বেরচ্ছিল… দরজা ভেজানো ছিল, ভিতরে ঢুকে দেখলাম…
শুভজিৎ থামিয়ে দেন যুবককে।
—দাঁড়ান, দেখছি।
দুটো তিনতলা বাড়ি। একটার পিছনে আরেকটা। সামনেরটা ২৪বি, পিছনেরটা ২৪এ। সামনের বাড়ির পাশ দিয়ে একটা সরু প্যাসেজ। যা পেরিয়ে পৌঁছতে হয় পিছনের ২৪এ-র সিঁড়ির কাছে। কৌতূহলী জটলা পেরিয়ে সিঁড়িতে পা রাখতে না রাখতেই গন্ধ নাকে ছিটকে আসে শুভজিতের। সেই গন্ধ, যার সঙ্গে ডাক্তার বা পুলিশের পরিচয় ঘটে যায় চাকরির শুরুতেই। একদম প্রথম দিকে গা গুলোত শুভজিতের, পচাগলা দেহ দেখলে। অবশ্য সয়েও গেছিল দ্রুত। এখন তো কিছুই মনে হয় না আর। অভ্যেস।
প্রতি তলায় একটা করে ফ্ল্যাট। তিনতলায় উঠে ফ্ল্যাটের অর্ধেক খোলা দরজার দিকে তাকান শুভজিৎ। কেউ খুলেছিল, না কি খোলাই ছিল, খোঁজ নেওয়ার জন্য অনেক সময় পড়ে আছে। আগে তো দেখা যাক, আদৌ খুন, আত্মহত্যা, না অন্য কিছু?
ফ্ল্যাট আয়তনে বড় নয় খুব। কত হবে? সাড়ে ছ’শো স্কোয়ারফুট মেরেকেটে। একটা মাঝারি মাপের ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং, একটা শোয়ার ঘর, বারান্দা একফালি। রান্নাঘর আর বাথরুম। এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক অবিকল নিল ডাউন অবস্থায় বসে রয়েছেন শোওয়ার ঘরে ঢোকার মুখে। বয়স মাঝপঞ্চাশ মনে হয় দেখে। আলতো পিঠ ঠেকে আছে দেওয়ালে। স্যান্ডো গেঞ্জি আর হাফপ্যান্ট পরে আছেন। ‘আছেন’ লেখা ভুল হল, ‘ছিলেন’। প্রাণহীন দেহে পচন ধরার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। দড়ি দিয়ে হাত বাঁধা পিছমোড়া করে। মুখে কাপড় গোঁজা। নাক থেকে রক্ত চুঁইয়ে পড়ে জমাট বেঁধেছে ঠোঁটের কোণে। দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন চোখে পড়ছে না তেমন। প্রতিরোধজনিত ক্ষত (defensive wound) অবশ্য আছে কিছু শরীরে। ছড়ে যাওয়ার দাগ, আঁচড়ের চিহ্ন কিছু। ধস্তাধস্তি হয়েছিল সম্ভবত খুনি বা খুনিদের সঙ্গে।
ফ্ল্যাটের বাইরে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন উৎসুক, তাঁদের জিজ্ঞেস করে মৃতের পরিচয় জানলেন শুভজিৎ। শ্যামপ্রসাদ রায়। একাই থাকতেন এবাড়িতে। আরও অনেক কিছু জানার আছে। তবে তার আগে তদন্তের প্রাথমিক কাজগুলো সেরে ফেলা দরকার। বডি পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠানো, ডগ স্কোয়াডকে খবর দেওয়া, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের তলব করা। এবং বড়বাবুকে ফোনে জানানো ঘটনাটা।
.
শ্যামপ্রসাদ রায় হত্যা মামলা। আজ থেকে এগারো বছর আগের ঘটনা। টালিগঞ্জ থানা। কেস নম্বর ২২২, তারিখ ১৬/৮/২০০৭। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায়। খুন এবং একই অপরাধের উদ্দেশ্যে একাধিকের সম্মিলিত পরিকল্পনা।
দক্ষিণ কলকাতার অভিজাত পাড়ার ফ্ল্যাটে একাকী বসবাসকারী প্রৌঢ় খুন। প্রতিক্রিয়ায় যা যা হওয়ার, হল। শহরে নিরাপত্তার অভাব নিয়ে কাগজে নিউজ়প্রিন্ট খরচ কিছু, এলাকায় পুলিশ পিকেট, ডিসি ডিডি, ডিসি সাউথ-সহ সিনিয়র অফিসারদের অকুস্থলে আসা একাধিকবার। ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের হোমিসাইড শাখার অফিসাররা পুরো দিনটাই কাটালেন পার্ক সাইড রোডে। বিকেল নাগাদ সিদ্ধান্ত হল, আপাতত টালিগঞ্জ থানাই থাকবে তদন্তের দায়িত্বে, প্রয়োজনে সাহায্য করার জন্য হোমিসাইড বিভাগ তো রইলই। তদন্তভার ন্যস্ত হল শুভজিতের উপরই। শুভজিৎ সেন, টালিগঞ্জ থানার তৎকালীন সাব-ইনস্পেকটর (বর্তমানে মেট্রো রেল পুলিশের ভারপ্রাপ্ত অফিসার-ইন-চার্জ)।
ময়নাতদন্তের ফল তেমনই, যেমনটা প্রত্যাশিত ছিল। ‘Death was due to the effects of violent Asphyxia by the process of smothering added with gagging and homicidal in nature.’ মুখে কাপড় গুঁজে, চেপে ধরে, শ্বাসরোধ। মৃতদেহের কাটাছেঁড়ার পর ডাক্তারবাবু আরও জানালেন, defensive wounds দেখে যা মনে হচ্ছে, একজন নয়, প্রৌঢ়কে কাবু করতে প্রয়োজন হয়েছিল একাধিক ব্যক্তির উপস্থিতির।
খুনটা কখন হয়েছিল? নির্দিষ্ট ডাক্তারি মতামত পাওয়া গেল, ময়নাতদন্তের আনুমানিক ছেষট্টি থেকে সত্তর ঘণ্টা আগে। থানায় ফোন এসেছিল ১৬ অগস্ট সকাল দশটা নাগাদ। তারপর দেহ উদ্ধারের পর পদ্ধতিগত খুঁটিনাটি মিটিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠাতে সন্ধে হয়ে গিয়েছিল। ১৭ তারিখ দুপুর গড়িয়ে গিয়েছিল পোস্টমর্টেম সম্পূর্ণ হতে। হিসেব করে যা দাঁড়াল, খুনটা হয়েছিল ১৪ অগস্ট সন্ধে ছ’টা থেকে রাত দশটার মধ্যে।
ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ফ্ল্যাটের ডাইনে-বাঁয়ে-উপর-নীচে খুঁটিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরও এমন কিছু পেলেন না, যা তদন্তে দিশা দেখাতে পারে। ‘ডেভেলপ’ করে ‘ম্যাচ’ করানোর মতো ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ফুটপ্রিন্ট নেই। শোওয়ার ঘরের আলমারি হোক বা অন্যান্য আসবাবপত্র, অক্ষত। আলমারির চাবি পড়ে আছে ড্রয়ারে। খুলে দেখা হল। অবিকৃত সব কিছু। জামাকাপড় নিপাট সাজানো, হাজার চারেক টাকা পড়ে আছে। দুর্মূল্য কিছু বাড়িতে ছিল, এমন ইঙ্গিত নেই। ফ্ল্যাট বৈভবহীন। ডাকাতির উদ্দেশ্যে খুন, ভাবার দূরতম কারণ নেই আপাতদৃষ্টিতে।
খুন হওয়ার প্রায় বাহাত্তর ঘণ্টা পরে পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না ঘ্রাণযোগ্য এমন কিছু, যা তদন্তে সাহায্যের হাত বাড়াবে। তবু এল পুলিশ কুকুর। নিয়মরক্ষার আসা-যাওয়া। কাজের কাজ হল না কিছু। মৃত প্রৌঢ়ের ব্যাপারে প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে শুভজিৎ প্রাথমিকভাবে যা জানলেন, এরকম:
শ্যামপ্রসাদ রায়ের বয়স হয়েছিল চুয়ান্ন। তিন ভাইয়ের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। মেজোভাই সলিলপ্রসাদের বয়স সত্তরের কাছাকাছি। সপরিবারে অবসরজীবন কাটান চেতলার জৈনুদ্দিন মিস্ত্রি লেনে। বড়ভাই থাকেন কলকাতার বাইরে বহু বছর ধরে।
তিন ভাই যে যার নিজের মতো থাকতেন। পরস্পরের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ-কথাবার্তা ছিল না বললেই চলে, জানালেন সলিলপ্রসাদ। বড়ভাই অসুস্থ। খবর দেওয়া হল, কিন্তু আসতে পারলেন না। কিন্তু মৃতের স্ত্রী-ছেলেমেয়ে কেউ?
জানা গেল, পেশায় উকিল শ্যামপ্রসাদবাবু আলিপুর কোর্টে প্র্যাকটিস করতেন। বিবাহিত। এক মেয়ে আছে। কিন্তু প্রায় দশ-বারো বছর হয়ে গেল স্ত্রী এবাড়ি ছেড়ে চলে গেছেন মেয়েকে নিয়ে। এখন থাকেন যাদবপুর থানা এলাকার গোলাম মহম্মদ শাহ রোডে দাদার আশ্রয়ে। মেয়ে বেহালার একটি স্কুলের হস্টেলে থেকে পড়াশুনো করে। ক্লাস এইট। আইনি ডিভোর্স দু’জনের হয়নি ঠিকই, কিন্তু সম্পর্ক ছিল না কোনও উভয় পক্ষে। মৃত্যুর খবরেও এলেন না স্ত্রী, মেয়েও না।
কেন মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ছেড়েছিলেন শ্যামপ্রসাদের স্ত্রী কৃষ্ণা? বনিবনার অভাব কী কারণে? সদুত্তর পাওয়া গেল না সলিলবাবুর কাছে। সাফ জানালেন, ভাইয়ের ব্যক্তিজীবন নিয়ে মাথা ঘামাননি কখনও।
গোলাম মহম্মদ শাহ রোড বেশি দূরে নয়। শুভজিৎ যখন কৃষ্ণাদেবীর বাড়িতে গিয়ে অতীত দাম্পত্য নিয়ে প্রশ্ন করলেন সন্ধের দিকে, মহিলা সোজাসাপটা জানিয়ে দিলেন, ‘উনি অত্যন্ত আত্মকেন্দ্রিক মানুষ ছিলেন। নিজেরটার বাইরে কিছু ভাবতে পারতেন না। চেষ্টা করেছিলাম অ্যাডজাস্ট করার। একটা পর্যায়ের পর পারিনি। এর বেশি বলার কিছু নেই। বহু বছর হল কোনও যোগাযোগ ছিল না। উনি কখনও খোঁজ নেননি। আমরা মা-মেয়েও কোনও উৎসাহ দেখাইনি।’
শুভজিৎ তবু খুঁচিয়েছিলেন মহিলাকে, ‘আচ্ছা ম্যাডাম, লাস্ট কোয়েশ্চেন, মানে, মিস্টার রায়ের কি চরিত্রের কোনও দোষ ছিল, আই মিন অন্য কোনও মহিলার সঙ্গে…?’ দৃশ্যতই বিরক্ত কৃষ্ণা থামিয়ে দিয়েছিলেন মাঝপথে। উত্তর দিয়েছিলেন কেটে কেটে, ‘যতদিন একসঙ্গে ছিলাম, চোখে পড়েনি অমন কিছু। পরের কথা বলতে পারব না।’ শুভজিৎ আর কথা বাড়াননি।
.
১৭ অগস্ট, শুক্রবার।
দেহ উদ্ধারের পরের দিনটা, সকাল থেকে সন্ধে অবধি শুভজিৎ কাটিয়েছিলেন ২৪এ এবং ২৪বি পার্ক সাইড রোডের ফ্ল্যাটগুলোর বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে। প্রত্যেকের বয়ান নিয়েছিলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে। ১৪ তারিখ বিকেল থেকে রাত, কে কোথায় ছিলেন, খোঁজ নিয়েছিলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। পাতা ভরতি হয়ে গিয়েছিল নোটবুকের। দিশা তবু ছিল দূর অস্ত। তথ্য অবশ্য মিলেছিল কিছু।
তথ্য বলতে, শ্যামপ্রসাদের বাবা সফল ব্যবসায়ী ছিলেন। কলকাতায় সম্পত্তি করেছিলেন প্রচুর। একাধিক বাড়ি কিনেছিলেন শহরে। তিন ভাইকে ভাগ করে দিয়েছিলেন অস্থাবর সম্পত্তি। পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ হিসেবে শ্যামপ্রসাদ পেয়েছিলেন পার্ক সাইড রোডের দুটো তিনতলা বাড়ি। প্রতি তলায় একটা করে ফ্ল্যাট। মোট ছ’টা। যার পাঁচটা বেচে দিয়েছিলেন। নিজে রেখেছিলেন একটা, ২৪এ-র তিনতলা।
পাড়াপ্রতিবেশীরা শ্যামপ্রসাদকে অন্তর্মুখী প্রকৃতির মানুষ হিসেবেই জানতেন। এ পাড়ায় ছিলেন প্রায় বছর কুড়ি। কারও সঙ্গেই ঘনিষ্ঠতা ছিল না। কোর্টে যাতায়াতের পথে বা বাজারহাট করার সময় পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হলেও ‘কী কেমন আছেন?’ আর ‘হ্যাঁ, চলছে’-র গণ্ডি পেরনোয় ঘোর অনীহা ছিল ভদ্রলোকের।
নিজের মতো থাকতে ভালবাসতেন। নিজে রান্না করে খেতেন। নিজেই বাসন মাজতেন, কাপড় কাচতেন। খবরের কাগজ নিতেন না। কাজের লোক বলতে কেউ ছিল না। একজন শুধু এসে ঘরদোর-বাথরুম পরিষ্কার করে দিয়ে যেতেন, সপ্তাহে দু’বার। শুধু ওঁর ফ্ল্যাটের নয়, সবারই। এই সাফাইকর্মীই ১৬ অগস্ট সকালে সাফসুতরো করতে এসে দরজার বাইরে থেকে দুর্গন্ধ পান এবং হইচই করে লোক জড়ো করেন।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে বাকি পাঁচটা ফ্ল্যাটের বাসিন্দাদের কাউকে সন্দেহ করার কোনও কারণ খুঁজে পেলেন না শুভজিৎ। তবে আরও খোঁজখবর করার আছে। একদিনে আর কী-ই বা বোঝা যায়? সোর্স লাগাতে হবে। যে যা বলেছেন সেদিন নিজের গতিবিধির ব্যাপারে, সেটা যাচাই করতে হবে।
এই যাচাই করার প্রক্রিয়াটা কী যে ভীষণ পরিশ্রমসাধ্য হত বছর বারো-তেরো আগে হলে! ভাগ্যিস মোবাইল ফোন ভারতে এসে গেছে নয়ের দশকের মাঝামাঝি, ১৯৯৫-তে। প্রাক্-মোবাইল যুগে ‘অ্যালিবাই’ যাচাই করতে কত না কাঠখড় পোড়াতে হত সেসময়ের গোয়েন্দাদের, ভাবলেই আঁতকে উঠতে হয় মোবাইল-উত্তর যুগের তদন্তকারীদের। যে যখন যেখানে ছিল বলেছে, সেখান থেকে অমুক সময়ে বেরিয়ে তমুক জায়গায় গিয়েছিল বলে দাবি করছে, সবটা মিলিয়ে নিতে হত জায়গায় গিয়ে, প্রত্যক্ষদর্শীদের খোঁজ করে।
আর মোবাইল এসে যাওয়ার পর? প্রযুক্তির আনুকূল্যে দ্রুত মিলবে CDR (Call Details Record) এবং টাওয়ার লোকেশন। যা নিমেষে প্রশ্নাতীত জানিয়ে দেবে, কে কখন কোথায় ছিলেন, কতক্ষণ ধরে কার সঙ্গে কথা বলেছেন বা মেসেজ চালাচালি করেছেন। কেউ মিথ্যে বলার চেষ্টা করলেই চেপে ধরা যায় নিমেষে, ‘টাওয়ার তো অন্য কথা বলছে!’
সন্ধেবেলা থানায় ফিরে নোটবই খোলেন শুভজিৎ। টাওয়ার সত্যিই অন্য কথা বলছে কিনা, জেনে যাওয়া যাবে স্বচ্ছন্দে। সবার মোবাইল নম্বর নিয়েছেন শুভজিৎ। পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন সংশ্লিষ্ট ‘সার্ভিস প্রোভাইডার’-দের কাছে। CDR হাতে এসে যাবে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। শুধু প্রতিবেশীদের নয়, আসবে শ্যামপ্রসাদের মোবাইল কলরেকর্ডও। যে বা যারাই ফ্ল্যাটে ঢুকে খুনটা করেছিল, তারা ফোনটা নিয়ে গেছে ওঁর। ফ্ল্যাটের কোথাও পাওয়া যায়নি। তারপর থেকে ফোন বন্ধ। রেকর্ডটা পেলে একটা ধারণা তো অন্তত হবে, ওঁর পরিচিত বৃত্তে কারা ছিলেন। আর কে বলতে পারে, অধরা সূত্রও চলে আসবে না হাতের মুঠোয়?
একগুচ্ছ কলরেকর্ডের পাতার পর পাতা ঘেঁটেঘুঁটে কাজের মধ্যে জানা গেল এই, প্রতিবেশীরা কেউ মিথ্যে বলেননি। যে যা বলেছিলেন ১৪ অগস্টের গতিবিধি নিয়ে, মিলছে হুবহু। এতেই যে সটান সন্দেহের বৃত্তের বাইরে ছিটকে গেলেন ওঁরা, এমন নয়। হতেই পারে, কেউ লোক লাগিয়ে খুনটা করিয়েছেন, এবং নিজের ‘অ্যালিবাই’ নিশ্ছিদ্র রেখেছেন। হতেই পারে, কারও সঙ্গে এমন কিছু শত্রুতা ছিল শ্যামপ্রসাদের, যা এখনও অজানা। সবে তো চব্বিশ ঘণ্টা হয়েছে।
শ্যামপ্রসাদের কলরেকর্ড বলছে, ১৪ তারিখ সকালে কোর্টে গিয়েছিলেন। বিকেল চারটে নাগাদ ফিরে আসেন বাড়িতে। সেই থেকে বাড়িতেই ছিলেন, বেরননি আর। গত এক মাসের কথোপকথন আর এসএমএস-এর খতিয়ান জানাচ্ছে, মোবাইলে দীর্ঘক্ষণের আলাপচারিতায় অভ্যস্ত ছিলেন না। কথাবার্তা মূলত পেশাগত পরিচিতির বলয়েই হত। মেসেজও যা কিছু, কাজের ব্যাপারেই। কোনও মহিলার সঙ্গে ফোন বা মেসেজ আদানপ্রদানের রেকর্ড নেই। বিপ্লব ঘোষ নামের একজনের সঙ্গে কথা বলতেন প্রায়ই, পাওয়া গেল রেকর্ড থেকে। সে-রাতেই শুভজিৎ ছুটলেন বিপ্লববাবুর কসবার বাড়িতে। যদি সূত্র মেলে কিছু।
সূত্র বলা যায় না সে অর্থে, কিন্তু একটা অজানা তথ্য পাওয়া গেল বাহান্ন বছরের বিপ্লববাবুর কাছে। ছোটখাটো ব্যবসা করেন। স্ত্ৰী-কন্যা নিয়ে সংসার। বিপ্লব জানালেন, শ্যামপ্রসাদের একটাই নেশা ছিল। ঘোড়দৌড়ের। বিপ্লববাবুও একই নেশায় আসক্ত এবং রেসকোর্সে যাতায়াতের সুবাদে ঘোড়দৌড়ের মাঠেই বছরদুয়েক আগে আলাপ শ্যামপ্রসাদের সঙ্গে। ফোনালাপ যেটুকু হত, সে ওই ঘোড়া নিয়েই। পরের শনিবারে কী কী রেস আছে, কোনটায় কোন ঘোড়া ফেভারিট, কত টাকা কোন রেসে কোন ঘোড়ার উপর লাগানো উচিত বা অনুচিত, এইসব।
রেসভাগ্য কেমন ছিল শ্যামপ্রসাদের? বিপ্লব জানালেন, ইদানীং কপাল মন্দ যাচ্ছিল শ্যামপ্রসাদের। গত কয়েক মাসে হারছিলেন লাগাতার। এবং মরিয়া হয়ে আরও বেশি টাকা লাগাচ্ছিলেন পরের রেসে। ভাগ্য তবু সহায় হচ্ছিল না কিছুতেই।
—জানেন শুভজিৎবাবু, আমি বারণ করেছিলাম। বুঝিয়েছিলাম, একটু বুঝেশুনে খেলতে। শ্যাম শুনত না। বলত, এখানে আজ যে ফকির, কাল সে রাজা।
—শেষ কবে দেখা হয়েছিল আপনার সঙ্গে?
—লাস্ট দুটো শনিবার যাইনি। শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। তার আগের শনিবার শেষ দেখা হয়েছিল। সেদিনও আমি বারবার বললাম ‘প্লেস’ খেলতে। কিন্তু শ্যামের জেদ, ও সেই ‘উইন’-ই খেলবে।
—‘প্লেস’ মানে?
—ওটা রেসের মাঠের ভাষা। ধরুন ৫ নম্বর ঘোড়ার উপর ‘প্লেস’ খেললেন। মানে, প্রথম তিনটে ‘প্লেস’, ফাস্ট-সেকেন্ড-থার্ডের মধ্যে আপনার ঘোড়া থাকলে লাভ। পাঁচশো লাগিয়ে হয়তো ছ’শো-সাড়ে ছ’শো এল।
—আর ‘উইন’?
—‘উইন’ মানে ৫ নম্বর জিতবেই ধরে আপনি টাকা লাগালেন। জিতলে লাগানো টাকা ডবল হয়ে যেতে পারে প্রায়, কিন্তু হারলে পুরো টাকাই জলে। ‘প্লেস’ খেললেও হারতেই পারেন, তবে ন্যাচারালি ঝুঁকি কম। কিন্তু ওই যে, শ্যামের জেদ…
—তা এত যে টাকা জলে যাচ্ছিল, সমস্যা হচ্ছিল না?
—হচ্ছিল তো। শ্যামের ওকালতির পসার তো তেমন একটা ভাল ছিল না। পৈতৃক সূত্রে পাওয়া ফ্ল্যাটগুলো বেচে ভালই টাকা পেয়েছিল। ব্যাংকে ছিল। সেই ভাঙিয়েই চলত। কিন্তু ওভাবে কি অনন্তকাল চলে বলুন? ইদানীং বলত, বাড়ির ছাদ আর চিলেকোঠার ঘরটা বেচে দেবে। খদ্দের খুঁজতে বলেছিল। এ নেশা ভয়ংকর নেশা শুভজিৎবাবু। কপাল খারাপ হলে রাজাকেও পথের ভিখিরি বানিয়ে ছাড়ে। কাগজে শ্যামের খবরটা দেখেছি। খুব খারাপ লেগেছে। কে মারল ওভাবে? জানতে পারলেন কিছু?
—সেটাই তো বোঝার চেষ্টা করছি। আপনার কী মনে হয়?
—আমি তো অবাক হয়ে গেছি খবরটা শুনে। শ্যামের কোনও শত্রু ছিল বলে তো মনে হয় না। টাকাপয়সাও যে অনেক ছিল, তাও নয়।
—অন্য কোনও দোষ, মানে মহিলা-টহিলা…
—দেখুন, আমি শ্যামকে দু’বছর ধরে জানি। ওঁর নারীবিষয়ে কোনও আগ্রহই ছিল না। ধ্যানজ্ঞান একটাই ছিল, রেসের মাঠ।
—একবার রেসকোর্সে যেতে চাই। কবে গেলে ভাল হয় বলুন তো? কথাটথা বলতে হবে একটু ওখানের স্টাফদের সঙ্গে।
—কালই যান না। আজ ১৭, শুক্র। কাল শনি। কাল চারটে রেস। দুপুর দুপুর চলে যেতে পারেন। আমি একজনের নাম-নম্বর দিয়ে দিচ্ছি। মণিময়। ওখানের মাঝামাঝি স্তরের স্টাফ। ভাল ছেলে। আপনাকে সব ঘুরিয়ে দেখাবে।
—আপনি যাবেন না কাল?
—না, কাল বাড়িতে লোকজন আসার কথা আছে কিছু। আর আমি এভরি স্যাটারডে যাইও না। শ্যাম রেগুলার ছিল। আমি মাসে বড়জোর দু’বার।
.
১৮ অগস্ট, শনিবার। রেসকোর্সে ভরদুপুর।
ঘোড়াগুলো ছুটছে। পাশাপাশি, ঊর্ধ্বশ্বাসে। ধুলো উড়ছে ট্র্যাকে এলোমেলো। শুরুর দিকে একে-অন্যের ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলা, তিরিশ-চল্লিশ মিটার পরেই ছবিটা বদলে গিয়ে ছিটকে বেরনো তিন-চারজনের দলের। এবং ফিনিশিং পয়েন্টে সবার আগে পৌঁছনোর মরণবাঁচন দৌড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গ্যালারির শব্দব্রহ্ম।
শুভজিৎ দেখতে থাকেন উদাসীন। এই প্রথম আসা রেসের মাঠে। কে জানে আর কতবার আসতে হবে? অথচ জায়গাটা কী সুন্দর! এত সবুজ চারদিকে। কী অপূর্ব লাগে এখান থেকে ভিক্টোরিয়াকে! ঘোড়দৌড়ে ন্যূনতম রুচি নেই শুভজিতের, কখনও ছিলও না। তবু ভাবেন, এই কেস মিটে গেলে এমনিই আর একদিন এলে হয়। খুনের তদন্তে নয়। স্রেফ সবুজ শুষে নিতে। কোনও এক উইকডে-তে, যেদিন কোনও দৌড় থাকবে না।
মণিময় এসে পড়েছেন। মধ্যতিরিশের সপ্রতিভ যুবক। চোখেমুখে বুদ্ধির ছাপ আছে। শুভজিৎ কোনও ভণিতা করেন না।
—বিপ্লববাবুর থেকে আপনার নম্বর পেয়েছি। বিপ্লব ঘোষ।
—হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, উনি ফোন করেছিলেন সকালে। শ্যামদার খুনের ব্যাপারে বলছিলেন…
—হ্যাঁ, সেই ব্যাপারেই আসা। উনি তো নিয়মিত আসতেন এখানে।
—ইয়েস স্যার, আমি এখানে বছরচারেক আছি। হি ওয়াজ় আ রেগুলার। প্রতি শনিবার দেখা হত। একটু ইনট্রোভার্ট প্রকৃতির লোক ছিলেন। বেশি কথা হত না।
—বুঝলাম। গত কয়েক সপ্তাহে বিশেষ কিছু লক্ষ করেছিলেন ওঁর ব্যবহারে? মানে যতটুকু কথা হত, যতটুকু বোঝা যায় বাইরে থেকে?
মণিময়ের উত্তরে স্নায়ু সামান্য সক্রিয় হয়ে ওঠে শুভজিতের।
—হ্যাঁ স্যার। বিপ্লবদা সকালে ফোন করার পর থেকেই ভাবছিলাম এটা। গ্যালারিতে আমাদের যে স্টাফরা থাকে, তারাও সবাই প্রায় চিনত শ্যামদাকে। ওরাও বলল।… জানি না এটা জরুরি কিনা…
—কী?
—তেমন কিছু নয়। আমার কাজটা বেসিক্যালি রেসের সময় গ্যালারিতে রেসকোর্সের কর্মীদের উপর খবরদারি করা। শেষ দুটো শনিবার শ্যামবাবুর সঙ্গে তিনটে ইয়ং ছেলেকে বসতে দেখেছিলাম। গল্পগুজব করছিলেন খুব। একটু অবাকই হয়েছিলাম। শ্যামবাবু তো বড় একটা মিশুকে প্রকৃতির ছিলেন না।
—তিনটে ছেলে? কেমন দেখতে? আগে দেখেছিলেন কখনও ওদের?
—স্যার, সেভাবে তো খেয়াল নেই। হাজার হাজার লোক আসে এখানে। বিপ্লবদা বললেন আর আপনি জানতে চাইছেন বলে ভেবেটেবে যেটুকু মনে পড়ছে, বয়স বেশি নয় ওদের। এই ধরুন তেইশ-চব্বিশ হবে। দু’জনের ছিপছিপে চেহারা। একজন একটু গোলগাল। মাঝারি হাইট সবার। এর বেশি মনে নেই স্যার।
যতটুকু মনে ছিল মণিময়ের, তা দিয়ে ‘Portrait Parle’ হয় না, হয় না চিহ্নিতকরণের জন্য ছবি আঁকানো। ছিপছিপে-গোলগাল-কমবয়সি-মাঝারি হাইট, এ দিয়ে হয়? এমন শ’খানেক লোক তো এই রেসকোর্সেই এ মুহূর্তে পাওয়া যাবে। অবশ্য চেহারার বিশদ বিবরণ পেলেই যে সূত্র মিলত কোনও, এমন না-ও তো হতে পারে। তিনটে ছেলের সঙ্গে পরপর দুটো শনিবার শ্যামপ্রসাদ গল্প করেছিলেন গ্যালারিতে, কী এমন অস্বাভাবিক? মণিময় হয়তো একটু বেশিই চিন্তা করে ফেলেছেন। এমন হয়, অভিজ্ঞতায় দেখেছেন শুভজিৎ। সবাই গোয়েন্দা হতে চায়। এবং সুযোগ পেলে কল্পনার উড়ান ব্যস্ত হয়ে পড়ে দুইয়ে দুইয়ে চার করতে।
—মণিময়বাবু, চললাম আজ। একটু চোখকান খোলা রাখবেন প্লিজ়। ওই ছেলেগুলোকে আবার যেদিন দেখবেন, সঙ্গে সঙ্গে ফোন করবেন।
—শিয়োর স্যার।
শুভজিৎ হাঁটতে শুরু করেন রেসকোর্সের মেন গেটের দিকে। নতুন দৌড়ের প্রস্তুতি ততক্ষণে শুরু হয়ে গিয়েছে। ধারাভাষ্যকার তারস্বরে উত্তেজনা আমদানি করছেন আপ্রাণ, ‘There you are! Lightning speed lined up at No. 1, Whispering Beauty at number 2 and watch out for Sweet Silver at 3…’
অন্য ঘোড়া, অন্য দৌড়।
.
১৯ অগস্ট, রবিবার।
শুধু একটা কেস নিয়ে পড়ে থাকলে চলে না থানার অফিসারদের। অন্য কেসের ডায়েরি লেখা আছে। ‘ল অ্যান্ড অর্ডার’ ডিউটি আছে। রোজকার রুটিন কাজ আছে। রবিবার ‘অফ’ ছিল। তবু থানায় এসেছেন শুভজিৎ বকেয়া কাজ সারতে। যা যা বেরিয়ে এসেছে এখনও পর্যন্ত খুনের তদন্তে, বাকি কাজ সেরে ঠান্ডা মাথায় সাজাতে থাকেন শুভজিৎ।
এক, শ্যামপ্রসাদের চরিত্র সম্পর্কে যা জানা যাচ্ছে রেস ছাড়া অন্য আসক্তি ছিল না। মহিলাঘটিত কিছু পাওয়া যাচ্ছে না।
দুই, শ্যামবাবুর অর্থকরী সমস্যা ছিল রেসের মাঠে বেপরোয়া টাকা ওড়ানোর ফলস্বরূপ। চিলেকোঠার ঘর সহ ছাদটা বেচে দেওয়ার কথা ভাবছিলেন। বিলাসী জীবনযাপন করতেন না।
এই লোককে খুন করে আর্থিক ভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা শূন্য। ফ্ল্যাটের ফরেনসিক পরীক্ষাও বলছে, আলমারি-ড্রয়ার বা অন্য জিনিসপত্র ছোঁয়ইনি খুনি বা খুনিরা। ছোঁয়ার মতো দামি কিছু ছিলই না আদপে। ‘মার্ডার ফর গেইন’ হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণতম।
তিন, সন্দেহভাজনদের তালিকা তৈরি করতে গিয়েই তো হোঁচট। কাকে সন্দেহ করবেন? প্রতিবেশীদের ‘অ্যালিবাই’ যাচাই করা হয়ে গেছে প্রযুক্তি-প্রমাণে। বিপ্লববাবু? যা বলেছেন, অক্ষরে অক্ষরে সত্যি, জানাচ্ছে মোবাইল-মানচিত্র। রইল বাকি রেসকোর্সের ওই তিনটে ছেলে। যাদের সম্পর্কে ধারণা করারই অবকাশ ঘটেনি। সন্দেহ তো পরের কথা।
চার, এবং সবচেয়ে মোক্ষম চার, মোটিভ? তদন্ত দু’ভাবে হয়। ‘কে’ থেকে ‘কেন’? আর, ‘কেন’ থেকে ‘কে’? অনেক মামলায় সন্দেহভাজন অপরাধী ধরা পড়ে যায় ঘটনাপরম্পরায় বা তথ্যসূত্রে। অপরাধের কার্যকারণ জানা যায় জেরায়। এসব ক্ষেত্রে আগে ‘কে’, পরে ‘কেন’। এ তদন্ত সরলরৈখিক।
জটিলতা আসে তখনই, যখন কূলকিনারা পাওয়া যায় না অপরাধীর, সংগৃহীত তথ্যের চুলচেরা বিশ্লেষণে পাওয়া যায় না কোনও সম্ভাব্য ইঙ্গিত। এই অবস্থাতেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ‘মোটিভ’। ‘কেন’ থেকে শুরু হয় ‘কে’-র সন্ধান। কেন খুন হলেন শ্যামপ্রসাদ? ‘কে মারবে’-র থেকেও বড়, কেন মারবে? টাকা ছিল না, যৌন-ঈর্ষার গল্প ছিল না, ব্যক্তিগত শত্রুতারও হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না কোনও। তাহলে?
.
২০ অগস্ট, সোমবার।
অপরাধ সে যেমনই হোক, তদন্তের গতিপথ কিছু ক্ষেত্রে ধার ধারে না যুক্তি-তর্কের। তোয়াক্কা করে না প্রথাগত ব্যাকরণের। সব নিয়ম, সব পদ্ধতিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কখনও কখনও কিনারাসূত্র অভাবিত সমাপতনে এসে পড়ে তদন্তকারীর নাকের ডগায়। শুধু সিনেমাতেই নয়, বাস্তবেও ঘটে এমন। কদাচিৎই, কিন্তু ঘটে।
সিনেমার প্রসঙ্গ উঠলই যখন, ‘সোনার কেল্লা’ ভাবুন। জয়পুরের রাস্তায় অটোসফরে লালমোহনবাবুর যদি চোখে না পড়ত সোনারংয়ের পাথরবাটির দোকান, যদি না দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন ফেলুদার, জয়সলমিরের কথা মাথায়ই আসত না ‘সোনার কেল্লা’-র সম্ভাব্য অবস্থান হিসেবে। ওই চোখে পড়াটা এবং দুয়ে-দুয়ে চারের সম্ভাবনার আবছা আভাস পাওয়ামাত্র অটো থামিয়ে প্রদোষ মিত্রের নেমে পড়া, রহস্যভেদে অন্যতম প্রধান deductive moment ওটাই। ‘Hajra’ আর ‘Hazra’-র তফাত তো আরও পরে। সার্কিট হাউসে, দুম করে ডক্টর হাজরার মুকুলকে নিয়ে বারমের রওনা হয়ে যাওয়ার খবর মন্দার বোসের থেকে পাওয়ার পর।
রক্তমাংসের গোয়েন্দাদের ভাগ্যে এহেন মুহূর্ত উদয় হয় কালেভদ্রে। কিন্তু যখন হয়, তখন ‘কোথা হইতে কী হইয়া’ যায়, হার মেনে যায় কল্পনার রহস্যকাহিনিও। ঠিক যেমনটা ঘটল ২০ অগস্টের সন্ধেয়।
রবিবার সারাদিন কাজ করেছেন। সোমবারও সাততাড়াতাড়ি এসেছেন থানায়, ডিসি সাউথের মাসিক ক্রাইম কনফারেন্সের প্রস্তুতি-পরিসংখ্যান তৈরি করতে সাহায্য করেছেন ওসি-কে। বড়বাবু সদয় হয়ে ছেড়ে দিয়েছেন সন্ধের মুখে, ‘বাড়ি যাও আজ। অত চাপ নেওয়ার কিছু নেই। সব কেস সাতদিনের মধ্যেই ক্র্যাক করতে হবে, এমন কথা নেই। দেখা যাক আর কয়েকদিন। ডিসি ডিডি ফোন করেছিলেন একটু আগে। ডেভেলপমেন্ট কিছু হল কিনা, জানতে চাইছিলেন।’
থানা থেকে বেরিয়ে মন একটু খারাপই হয়ে যায় শুভজিতের। গোয়েন্দাপ্রধানের এই ‘জানতে চাওয়া’-র অর্থ বুঝতে অসুবিধে হয় না। অগ্রগতি যদি দ্রুত না হয়, লালবাজারের গোয়েন্দাবিভাগ দায়িত্ব নেবে তদন্তের। স্বাভাবিক, এটাই প্রথা। হইচই ফেলে-দেওয়া মামলায় দ্রুত কিনারা থানাস্তরে সম্ভব না হলে এটাই হয়ে থাকে।
শুভজিৎ থাকতেন উলটোডাঙার পুলিশ আবাসনে। বাড়ি থেকে থানায় যাতায়াত মোটরসাইকেলে। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে গিরিশ পার্কের কাছাকাছি পৌঁছনোর সময় শুভজিতের মনে হল, একবার সুরজিতের ঠেকে এক কাপ চা খেয়ে ফেরা যাক। একটু আড্ডা দিলে মাথাটা হালকা হতে পারে।
সুরজিত রায়ের সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয় শুভজিতের। ভদ্রলোক বেশ কিছুটা ছোট বছর চল্লিশের শুভজিতের থেকে। গিরিশ পার্ক এলাকায় একটা শরীরচর্চার আখড়া চালান। যেখানে রোজ সন্ধেয় ছেলেছোকরারা আসে ঘাম ঝরাতে। সুরজিতের গ্রহরত্নের কারবারও আছে একটা। খুব বড়সড় কিছু ব্যবসা নয়, মাঝারিই। সুরজিতের ঠেকে মাঝে মাঝে অফিসফেরত ঢুঁ মেরে একটু গল্পগুজব করে আসেন শুভজিৎ।
—আরে শুভজিৎদা, অনেকদিন পরে? খবর কী?
—এই তো, চলছে ভাই। আসা হয়নি মাসখানেক হল, ভাবলাম একটু চা খেয়ে যাই।
—বেশ করেছ, কিন্তু তোমাকে এত উস্কোখুস্কো দেখাচ্ছে কেন? শরীর ঠিক আছে তো?
—শরীর তো ঠিকই আছে, মনটাই বিগড়ে আছে। একটা খুনের মামলা নিয়ে ফেঁসে আছি। একজন বয়স্ক মানুষ নিজের ফ্ল্যাটে…
—হ্যাঁ হ্যাঁ, কাগজে দেখেছি। ওটা তুমি ইনভেসটিগেট করছ?
—আর বলো কেন? তিনদিন হয়ে গেল, কোনও লিড নেই।
—সবে তো তিনদিন, পেয়ে যাবে ঠিক।
—সব অ্যাঙ্গল মোটামুটি দেখা হয়ে গেছে। তবু এগোনো যাচ্ছে না। এসব মামলায় কী জানো, শুরুর দিকে ‘লিড’ পেয়ে গেলে ভাল। যত দেরি হয়, তত মুশকিল হয়ে যায়। একটা কেসের উপরই তো আর দিনের পর দিন ফোকাস করা যায় না।
—হুঁ, নাও, চা খাও।
চায়ের কাপে আনমনা চুমুক দেন শুভজিৎ। চানাচুরের প্লেট এগিয়ে দিতে দিতে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেন সুরজিৎ।
—অত চিন্তা কোরো না। হয়ে যাবে ঠিক। এক এক সময় লাক খারাপ যায়।
—যা বলেছ। কপাল খারাপ। নির্ঘাত রাহুর দৃষ্টি পড়েছে, বুঝলে? দাও না একটা ভাল দেখে আংটি-টাংটি।
সুরজিৎ হেসে ফেলেন।
—সে না হয় দেব দেখেশুনে। আংটির কথায় মনে এল, যা দিনকাল পড়েছে! সেদিন যা কাণ্ড হল…
—কী?
—আর বোলো না। এই তো দিনতিনেক আগে হবে, দুটো ছেলে একটা আংটি নিয়ে এখানে এসে বলে কী, ‘এটার দাম এক কোটি টাকা। আপনার তো স্টোনের ব্যবসা আছে। খদ্দের জোগাড় করে দিতে পারেন?’
—কোটি টাকা?
—আরে, আমি তো হাঁ! বলে কী! আংটিটা অবশ্য সত্যিই অন্যরকম দেখতে। কারুকাজ আছে অনেক। মধ্যের পাথরটা বেশ বড়, আর খুব ঝকমকে। দেখলে হিরে বলে ভুল হতে পারে। তবে হাতে নিয়ে একটু উলটেপালটে দেখেই বুঝলাম, খুব দামি কিছু নয়। হিরে তো নয়ই। দাম মেরেকেটে ওই দশ-বিশ হাজার হতে পারে ম্যাক্সিমাম।
আংটির গল্পে কোনও উৎসাহ পান না শুভজিৎ। স্রেফ ভদ্রতার খাতিরেই বলেন, ‘তারপর?’
—তারপর আর কী? বললাম, ‘ভাই, এর দাম এক লাখও হবে না, কোটি তো অনেক দূরের ব্যাপার। বড়জোর হাজার দশেক পেতে পারো।’ শুনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল দু’জন। বললাম, ‘কোথায় পেয়েছ এটা?’
—কী বলল?
—কিছু বলল না। হনহন করে বেরিয়ে গেল।
—চোরাই মাল হতে পারে। কোথাও থেকে হাতিয়েছে, তারপর এখানে-সেখানে আগডুম-বাগডুম দাম হেঁকে বাজিয়ে দেখছে।
—দেখেশুনে কিন্তু চোর মনে হয়নি। ভদ্রঘরের ছেলে বলেই মনে হল।
—আগে দেখেছ ওদের? মানে আগে এসেছিল কখনও এখানে?
—না না, আগে দেখিনি। কেন?
—না, এমনিই। চেহারার ডেসক্রিপশনটা ভাল করে জেনে নিতাম আর কী, ডিডি-তে একটা anti-fraud সেকশন আছে, ওরা এসব গ্যাং-এর ব্যাপারে খবরটবর রাখে, জাস্ট বলে রাখতাম। যাক গে ছাড়ো, উঠি আজ…
—আমার তো খুব ডিটেলে মনে নেই, তবে দাঁড়াও দাঁড়াও, সাত্যকিকে ডাকি। সাত্যকির সঙ্গেই তো এসেছিল ওরা। সাত্যকি, এই সাত্যকি!
লাগোয়া ঘরটায় চলছিল যুবকদের রোজকার শরীরচর্চা। সেখান থেকে সাড়া দেয় এক যুবক।
—হ্যাঁ সুরজিৎদা …
—আয় না একবার এখানে…
পুলিশের পোশাকে শুভজিৎকে দেখে হঠাৎই একটু থমকে যায় যুবক। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় সুরজিতের দিকে।
—হ্যাঁ রে, ওই সেদিন তোর সঙ্গে দুটো ছেলে এসেছিল না… ওই যে রে, আংটি নিয়ে একটা…
‘আংটি’ শব্দটা সুরজিৎ উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই চোখমুখ সাদা হয়ে যায় সাত্যকির। শুভজিৎ লক্ষ করেন, হাত-পা কাঁপছে ছেলেটির। কী হল হঠাৎ? সুরজিৎও ঘাবড়ে যান সাত্যকির চেহারা দেখে।
—শরীর খারাপ লাগছে নাকি রে? ইনি টালিগঞ্জ থানার অফিসার, ওই ছেলেদুটোর ব্যাপারে জানতে চাইছিলেন।
বলতে না বলতেই হাউহাউ করে কেঁদে ফেলে সাত্যকি। কান্নায় জড়িয়ে যায় ভয়ার্ত গলার স্বর।
—স্যার… আমি যাইনি সেদিন। খুনে আমি ছিলাম না! বিশ্বাস করুন, আমি যাইনি ওদের সঙ্গে! ওরা মেরেছে।
শুভজিৎ শুনলেন, এবং উঠে দাঁড়ালেন চেয়ার ছেড়ে। ক্লান্তি অন্তর্হিত। শ্রান্তি নিরুদ্দেশ। খুন? ওরা? সেদিন? সুরজিৎ কিছু বলতে যাওয়ার আগেই থামিয়ে দিলেন।
—সুরজিৎ, বাকিদের চলে যেতে বলো আজ। আরেক কাপ চা হলে ভাল হয়। এই ছেলেটার সঙ্গে কথা বলার আছে। সময় লাগবে।
সময় লাগল না বেশি। পরের যে বাক্যটি সাত্যকির মুখ থেকে বেরল, তাতে শুভজিৎ বুঝলেন, শ্যামপ্রসাদ হত্যা মামলা গোয়েন্দাবিভাগের হাতে যাচ্ছে না। ভাগ্য ফেরাতে আংটিরও প্রয়োজন পড়ছে না আপাতত।
—স্যার, ওরাই বলেছিল, আংটির খদ্দের খুঁজে দিতে। আমি সুরজিৎদার কাছে নিয়ে এসেছিলাম। ওরা বলেছিল, শ্যামদার আংটিটার দাম নাকি এক কোটি। কিন্তু আমি যাইনি স্যার সেদিন, খুনে আমি ছিলাম না।
.
সাত্যকি মল্লিক। বয়স বছর চব্বিশ। মধ্য কলকাতার পোস্তা এলাকার বনেদি এবং সম্পন্ন পরিবারের সন্তান। আশৈশব সঙ্গী থেকেছে সচ্ছলতা। স্কুলজীবন কেটেছে পার্ক সার্কাসের ডন বসকোতে। সপ্রতিভ চেহারা, কথাবার্তায় চৌকস।
স্কুল-কলেজের পাট চোকানোর পর আপাতত কর্মহীন। কিন্তু বেকারত্ব কোনও আঁচড় বসাতে পারেনি আয়েশি জীবনযাপনে। অফুরান হাতখরচা, যার অর্ধেক ব্যয় হত ইয়ারদোস্তদের সঙ্গে খানাপিনায়, আর বাকি অর্ধেক রেসের মাঠে।
যে দুই বন্ধু নিয়মিত সাত্যকির সঙ্গী হত ঘোড়দৌড়ের মাঠে, তাদের মধ্যে একজনের নাম অরিন্দম। অরিন্দম ঘোষ ওরফে বাবলা। বয়স ২৬, টালিগঞ্জ রোডের বাসিন্দা। বিবাহিত, স্ত্রী এবং দেড় বছরের কন্যাসন্তান আছে। উপার্জন? টুকটাক জমি-বাড়ির দালালি করে যতটুকু হয়। অর্থাভাব ছিল। চটজলদি বড়লোক হওয়ার বাসনাও। অরিন্দমও ডন বসকোরই প্রাক্তনী।
রেসের মাঠে সাত্যকি-অরিন্দমের অন্য সঙ্গীর নাম অম্লান দত্ত। বয়স সবে কুড়ি পেরিয়ে একুশ। বাড়ি রসা রোডে। বেকার। অরিন্দম ঘোষের বন্ধু একসঙ্গে ফুটবল খেলার সূত্রে। পড়াশুনার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছিলেন অম্লান। ‘বাবার হোটেলেই’ দিন গুজরান। বাকি দু’জনের পকেটের জোর ছিল না, সাত্যকিই জোগাতেন ফুর্তির রসদ। পোস্তা এলাকার তারাসুন্দরী পার্কে নিয়মিত আড্ডা বসত ত্রয়ীর। আর মাসে অন্তত দুটো শনিবার গন্তব্য ছিল রেসকোর্স।
রেসকোর্সেই ত্রয়ীর আলাপ শ্যামপ্রসাদ রায় বা ‘শ্যামদা’-র সঙ্গে। কথায় কথায় একদিন শ্যামপ্রসাদ তিনজনকে বলেন, তাঁর কাছে একটা বহুমূল্য আংটি আছে। পৈতৃক সূত্রে পাওয়া। ‘অ্যান্টিক ভ্যালু’ প্রচুর এ আংটির। আংটির মধ্যে একটা দুর্মূল্য পাথর বসানো। ওই পাথরের জন্যই আংটিটার দাম প্রায় এক কোটি। একা মানুষ, বয়স হয়েছে। আজ আছেন, কাল নেই। আংটিটা বিক্রি করে দিতে চান এবার, খদ্দের খুঁজছেন। আশি-নব্বই লাখ পেলেও দিয়ে দেবেন।
প্রথমে বিশ্বাস হয়নি সাত্যকি-অরিন্দমদের। এত দামের আংটি আবার হয় নাকি? শ্যামপ্রসাদ ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পেরে বলেন, ‘তোমরা বাড়িতে এসো একদিন। দেখলে বুঝবে।’
—দেখে কী বুঝেছিলে?
বিধ্বস্ত সাত্যকির কাছে জানতে চান শুভজিৎ।
—বাড়িতে গিয়েছিলাম আমরা তিনজন। দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল স্যার। সত্যিই অমন আংটি দেখিনি আগে। শেপটা hexagonal, মধ্যের পাথরটা থেকে যেন আলো ঠিকরোচ্ছে। আমরা ভেবেছিলাম, শ্যামদা নির্ঘাত দামটা বেশি বাড়িয়ে বলছে, তবে এর দাম চল্লিশ-পঞ্চাশ লাখ হতেই পারে।
—তারপর?
—বলছি স্যার। আমরা সন্ধেবেলা পোস্তার পার্কে আড্ডা দিতাম প্রায় রোজ। সঞ্জয়দাও থাকত।
—কে সঞ্জয়?
—সঞ্জয়দা। ব্যান্ডেলের ছেলে। আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড়। বড়বাজারে আসত টুকটাক ব্যবসার কাজে। এখানে ওর এক আত্মীয়ের বাড়িও আছে। পার্কেই আলাপ।
—বেশ…
—সঞ্জয়দাকে বললাম। সব শুনে বলল, ‘এক কোটি হয়তো হবে না, কিন্তু যদি ধর পঁচিশ-তিরিশ লাখও হয়, আংটিটা হাতাতে পারলে আমাদের ভাগ্য খুলে যাবে। তোরা ভদ্রলোককে বল, এখানে আংটিটা নিয়ে আসতে কোনও একদিন। বল, কাস্টমার পাওয়া গেছে। আংটি দেখতে চাইছে। আমি লোক ফিট করছি, যারা রাস্তায় ছিনতাই করে নেবে আংটিটা। নিয়ে পরে আমাদের দিয়ে দেবে। আর আমরাও কেস খাব না। ছিনতাই যারা করবে, তাদের কয়েক হাজার টাকা ঠেকিয়ে দেব।’
—তারপর?
—শ্যামদাকে রেসকোর্সে বললাম একদিন। উনি বললেন, অত দামি জিনিস বাইরে নিয়ে বেরবেন না। কাস্টমারকে বাড়িতে আসতে বলো।
—তোমরা কী করলে এরপর?
—সঞ্জয়দা সব শুনে বলল, ‘এক কাজ কর। চল, ওঁর বাড়ি যাই। আমি কাস্টমার সাজব। আমাকে তো চেনে না। ভালয় ভালয় দিলে ভাল, নয় তো কেড়ে নেব। আংটিটা পেলে লাইফ বদলে যাবে আমাদের।’
—হুঁ…
—রেসকোর্সে শ্যামদার সঙ্গে দেখা হল গত শনিবার।
—মানে ১১ তারিখ?
—তাই হবে স্যার, তারিখ মনে নেই। শ্যামদাকে বললাম, ‘কাস্টমার পাওয়া গেছে। আপনার বাড়িতে আনব?’ উনি বললেন, ‘ঠিক আছে। মঙ্গলবার বিকেলে আনো।’
—মানে চোদ্দো তারিখ।
—তাই হবে স্যার। কিন্তু আমার ব্যাপারটা ভাল লাগছিল না শুরু থেকেই। আমি বলে দিয়েছিলাম, যেতে পারব না। নেমন্তন্ন আছে। আমি যাইনি স্যার।
—যাওনি?
—না স্যার, বিশ্বাস করুন। সঞ্জয়দা আরও চারজনকে জুটিয়েছিল।
—কোন চারজন?
—বলছি। কালো স্যান্ট্রো করে ওরা শ্যামদার বাড়ি গিয়েছিল স্যার। আগের রাতে পার্কে সব কথা হয়েছিল। পোস্তাতে একজন ব্যবসায়ী আছে। রাজেশ নাম। ওর ড্রাইভারের নাম রাম। ওই গাড়ি করে শ্যামদার বাড়ি নিয়ে গিয়েছিল।
—চারজনের একজন হল, বাকি তিন?
—দু’জনের নাম বিজয়। একজন বিজয় রায়। হাওড়ায় বাড়ি। লিলুয়া বোধহয়। আরেকজনের পদবি সিং। বিজয়বাহাদুর সিং। বড়বাজারে শাড়ির দোকানে অর্ডার সাপ্লাই করে। সঞ্জয়দা চিনত এদের।
—আরেকজন?
—অমিত নাম। কী করে জানি না। ওরা জানে। আগে এক-দু’বার দেখেছি। কাছেপিঠেই থাকে। এগজ়্যাক্ট জানি না।
নির্দিষ্ট ভাবে সব জানার দরকারও ছিল না আর। সাত্যকির থেকে শুভজিৎ নিয়ে নিলেন অম্লান-সঞ্জয়-অরিন্দম ঘোষের মোবাইল নম্বর। কাজ বলতে বাকি ছিল একে একে সাতজনকে ধরা। সে-রাতে আর বাড়ি ফেরা হল না শুভজিতের। ফিরলেন থানায়। প্রথমেই হানা দিলেন টালিগঞ্জে অরিন্দম ঘোষের বাড়ি। বাড়িতে নেই। অরিন্দমের বাবা পুলিশে চাকরি করতেন। অবসরপ্রাপ্ত সাব-ইনস্পেকটর। জানতে চাইলেন শান্ত ভাবে, ‘বাড়িতে পুলিশ কেন?’ সব শুনে ততোধিক শান্ত ভঙ্গিতে বললেন, ‘ছেলেটা নষ্ট হয়ে গেছে জানতাম এমন ছেলে থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। কোথায় আর যাবে? আশেপাশেই থাকবে। রাত দেড়টা-দুটোর আগে তো বাড়ি ফেরে না। ফোন নম্বরটা দিয়ে যান আপনার, বাবলা বাড়ি ফিরলেই খবর দেব।’
—একটা ছবি পাওয়া যাবে আপনার ছেলের?
বিনা বাক্যব্যয়ে ছেলের ছবি এনে শুভজিতের হাতে তুলে দিয়েছিলেন অরিন্দমের বাবা। বাড়ি ফেরার আগেই ধরা পড়ল অরিন্দম। ফোনের উপর প্রযুক্তি-প্রহরা চালু হয়ে গিয়েছিল সে-রাতেই, জানা যাচ্ছিল গতিবিধি। ভবানী সিনেমা থেকে নাইট শো দেখে বেরনোর মুখে ধরা হল। টালিগঞ্জ থানায় জিজ্ঞাসাবাদ চলল রাতভর। খুনের বৃত্তান্ত জানা গেল বিস্তারিত।
ছকের আসল কারিগর ছিলেন ব্যান্ডেলের সঞ্জয় ব্যানার্জি। তারাসুন্দরী পার্কের আড্ডায় অরিন্দমদের কাছে আংটি-বৃত্তান্ত শোনার পর সঞ্জয়ই মাথায় ঢোকান বাকিদের, আংটিটা হাতাতে পারলে সারা জীবন আর কারও কোনও চিন্তা থাকবে না। সঞ্জয়ই জুটিয়েছিলেন কুকর্মের আরও চার শরিককে।
বিজয়বাহাদুর সিং ওরফে বাদল, বড়বাজারের একটা শাড়ির দোকানের অস্থায়ী কর্মী। লিলুয়ার বিজয় রায়, যার বড়বাজারেই ফলের রসের ছোট দোকান। হরিরাম গোয়েঙ্কা স্ট্রিটের বাসিন্দা কুড়ি বছরের বেকার যুবক অমিত সিং। এবং যেহেতু কাজ হাসিল করার পর পালাতে হবে দ্রুত, গাড়ি দরকার। স্থানীয় ব্যবসায়ী রাজেশ প্রসাদের ড্রাইভার রামকুমার মণ্ডলকে লোভ দেখিয়ে দলে টেনেছিলেন সঞ্জয়।
চিত্রনাট্য ছিল এরকম— শ্যামপ্রসাদ কোর্ট থেকে সাধারণত ফিরে আসেন পাঁচটার মধ্যে। সাড়ে তিনটে থেকে চারটের মধ্যে মালিকের কালো স্যান্ট্রো গাড়ি নিয়ে রামকুমার পৌঁছবে পার্কের কাছে। মালিককে আগের রাতে বলে রাখবে গাড়ি সার্ভিসিং-এর কথা। বাকিরা অপেক্ষা করবে পার্কে।
পৌনে পাঁচটার মধ্যে রাসবিহারী মোড়ের কাছে পৌঁছনো হবে। পৌনে ছ’টা থেকে ছ’টার মধ্যে এক এক করে সবাই পৌঁছে যাবে তিনতলায় শ্যামপ্রসাদের ফ্ল্যাটের সামনে। রামকুমার গাড়ি নিয়ে অপেক্ষায় থাকবেন শরৎ বোস রোডের মুখে। সঞ্জয় যাবেন ‘কাস্টমার’ সেজে। আংটিটা দেখতে চাইবেন। এবং কিছুক্ষণ ‘নাম-কা-ওয়াস্তে’ দরদামের পর বলবেন, বাইরে ভাল দোকান থেকে যাচাই করে দু’-একদিন পরে আংটি ফেরত দিয়ে যাবেন। জানা কথা, শ্যামপ্রসাদ এ প্রস্তাবে রাজি হবেন না। তখন জোর করে কেড়ে নিতে হবে আংটি।
অরিন্দমকে বয়ানের মাঝপথেই থামান শুভজিৎ।
—শুধু কেড়ে নিয়ে পালালে তো সেটা একরকম হত। কিন্তু খুন…
—না স্যার, বিশ্বাস করুন, আমি জানতাম, আংটি নিয়ে পালিয়ে যাব। সঞ্জয়দা আর অম্লান যে অন্য প্ল্যান করেছে, ব্যাগে করে নারকেল দড়ি আর মুখে গোঁজার কাপড় নিয়ে গেছে, জানতাম না। বোকার মতো গেলাম ওদের সঙ্গে, ভুল হয়ে গেছে স্যার। সাত্যকি কিছু একটা আঁচ করে আগের রাতে আমাকে বলেছিল, ‘যাস না বাবলা, এই সঞ্জয় লোকটা ক্রিমিন্যাল টাইপের মনে হচ্ছে। উলটোপালটা কিছু করলে ফেঁসে যাব।’
—বন্ধুর কথা শুনলে খুনের দায়ে জেল খাটতে হত না, এখন বলে আর কী লাভ?
—স্যার, ও কিছুতেই যেতে রাজি হল না। নেমন্তন্ন আছে বলে কাটিয়ে দিল। বলল, টাকার ভাগ লাগবে না ওর। বড়লোকের ছেলে, টাকার অভাব নেই। আমি লোভ সামলাতে পারলাম না। সঞ্জয়দা বলেছিল, এক একজনের ভাগে কম করে পাঁচ-সাত লাখ করে পড়বে। টানাটানির সংসার, জমির দালালি করে আর কত হয়? বাবার পেনশনের টাকাতেই সংসারটা চলে। কিন্তু শ্যামদাকে খুন করার কথা কখনও মাথায় ছিল না, বিশ্বাস করুন।
—মাথায় এসেছিল কি না সেটা তো এখন আর জরুরি নয়…
—আমার কথাটা একটু শুনুন স্যার সঞ্জয়দা আংটিটা হাতে নিয়ে শ্যামদাকে বলল, ‘দাদা,
দু’-একদিন পরে ফেরত দিয়ে যাব এটা। টাকাপয়সার কথা সেদিনই ফাইনাল করব। আগে তো দেখি সত্যিই যত বলছেন, তত দাম কিনা।’ শ্যামদা এই শুনেই রেগে আগুন হয়ে চিৎকার শুরু করল, ‘চালাকি পেয়েছেন? ফেরত দিন আমার জিনিস। আমি বিক্রি করব না আংটি।’
—তারপর কী হল?
—আমার দিকে তাকিয়ে শ্যামদা বলল, ‘এসব কী ব্যাপার অরিন্দম? এ কেমন কাস্টমার নিয়ে এসেছ? আর এত লোক নিয়েই বা এসেছ কেন?’
—তারপর?
সঞ্জয়দা ঝাঁপিয়ে পড়ল শ্যামদার উপর। ওর সঙ্গে অম্লান-অমিত আর দুই বিজয়। আমিও যোগ দিলাম স্যার। তখনও ভাবিনি, শ্যামদাকে মেরেই ফেলা হবে। সঞ্জয়দা বলতে থাকল, ‘একে বাঁচিয়ে রাখলে আমাদের সর্বনাশ হবে। পুলিশকে সব বলবে। ধরা পড়বই কাল নয় পরশু।’ আমি ভাবলাম, ঠিকই তো বলছে… তারপর তো জানেন স্যার, সবাই মিলে হাত-পা বেঁধে, মুখে কাপড় গুঁজে…
—আংটিটা কোথায়? আর শ্যামবাবুর মোবাইল?
—মোবাইলটা ফেরার পথে গাড়ি থামিয়ে আছড়ে ভেঙে ফেলেছিল সঞ্জয়দা। বলেছিল, ‘এটা রাখা রিস্কি। পুলিশ ক্লু পাবে।’ আংটি সঞ্জয়দার কাছে আছে। পরদিন সকালে সাত্যকি সব শুনে বলল, ‘তোকে আগেই বলেছিলাম বাবলা, যাস না। এখন তো পুলিশ পিছনে লেগে যাবে।’ অম্লান আর আমি বললাম, ‘যা হওয়ার হয়ে গেছে। আংটিটা বেচে টাকা যা পাব, নিয়ে পালিয়ে যাব কলকাতার বাইরে।’ সাত্যকি যেখানে জিম করতে যেত, তার মালিকের জেম-জুয়েলারির কারবার ছিল। বললাম, একবার আংটিটা ওঁকে দেখানোর ব্যবস্থা করতে।
—সাত্যকি রাজি হল?
—প্রথমে হচ্ছিল না। আমরা জোরজার করায় নিমরাজি হল। পরদিন সন্ধেয় আংটিটা নিয়ে গেলাম। জিমের মালিক ভদ্রলোক দেখেশুনে বললেন, দাম বড়জোর হাজার দশেক হবে। আমরা চলে এলাম মন খারাপ করে। বুঝলাম, শ্যামদাই কোনও শাঁসালো খদ্দেরকে ঠকানোর মতলব এঁটেছিল আমাদের থ্রু দিয়ে।
—এরপর?
—সঞ্জয়দা সন্ধেবেলা পার্কে এসেছিল। বললাম সব। শুনে বলল, ‘আমাকে আংটিটা দে। ব্যান্ডেলে ভাল দোকান আছে। আমি ওখানে দেখাব আংটিটা।’ দিয়ে দিলাম। তারপর থেকে সঞ্জয়দার সঙ্গে কথা হয়নি আর। ফোন বন্ধ।
.
রাজকুমার, অমিত, বিজয়বাহাদুর এবং বিজয় রায়, এই চারজনকে ধরাটা কষ্টসাধ্য হল না বিশেষ। এক সপ্তাহের মধ্যেই গ্রেফতার হল। সঞ্জয় ছিলেন ধূর্তচূড়ামণি। কাগজে বেরিয়েছিল খুনের কিনারার খবর। জানতেন, পুলিশ হানা দেবেই ব্যান্ডেল স্টেশন রোডের বাড়িতে। পালিয়েছিলেন, মোবাইল দিনভর বন্ধ রাখতেন। চালু করতেন দিনে এক বা দু’বার। সঞ্জয়ের বাড়ি থেকে জোগাড় করা হয়েছিল ছবি। যা ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সোর্সদের মধ্যে।
আংশিক প্রযুক্তি-সূত্র, আংশিক সোর্সের খবরের ভিত্তিতে সঞ্জয় ধরা পড়লেন ৮ সেপ্টেম্বর। আমহার্স্ট স্ট্রিটের ‘ক্রাউন লজ’ থেকে। যেখানে ‘মনোজিৎ ব্যানার্জি’ নামে উঠেছিলেন ৬ সেপ্টেম্বর। আসাম থেকে আসা ব্যবসায়ীর পরিচয়ে।
আংটি পাওয়া গেল না সঞ্জয়ের কাছেও। গেল কোথায়? সঞ্জয়ের বয়ান, ‘আমি দু’-একটা দোকানে যাচাই করে দেখেছিলাম স্যার। বলল, পাথরটা দেখতেই দামি হিরের মতো। হিরে নয়। ভাবলাম, আরও কয়েকটা জায়গায় দেখাব। তার মধ্যেই কাগজে দেখলাম, বাবলা ধরা পড়ে গেছে। আংটিটা বেচা রিস্কি হয়ে যেত। নিজের কাছে রাখলেও প্রমাণ থেকে যেত। গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিলাম স্যার।’
প্রত্যক্ষদর্শীহীন অপরাধ। পুলিশের কাছে দেওয়া বয়ানের অকাট্য প্রমাণমূল্য নেই আদালতে। যতক্ষণ না পারিপার্শ্বিক প্রমাণের সমর্থন থাকে ঠাসবুনোট। শুভজিতের পেশ করা চার্জশিটে ঘটনা-পরম্পরা উঠে এল চিত্রবৎ।
বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল রাজেশ প্রসাদের কালো স্যান্ট্রো গাড়িটা। রাজেশ নিজের সাক্ষ্যে জানালেন, গাড়িটা সার্ভিসিং-এর অজুহাতে ১৪ অগস্ট নিয়ে বেরিয়েছিলেন রামকুমার। সাত্যকি মল্লিক বিচারকের কাছে জবানবন্দি দিলেন (judicial confession, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৬৪ ধারায়)। যাতে ধরা থাকল শ্যামপ্রসাদের সঙ্গে রেসের মাঠের আলাপ হওয়া থেকে শুরু করে আংটি হাতানোর পরিকল্পনা, সব। সুরজিৎ আদালতে চিহ্নিত করলেন অরিন্দম ঘোষ এবং অম্লান দত্তকে। আমহার্স্ট স্ট্রিটের ‘ক্রাউন লজ’ থেকে বোর্ডার্স রেজিস্টার বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। যেখানে ‘মনোজিৎ ব্যানার্জি’ নামে সই করেছিলেন সঞ্জয়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সে হস্তাক্ষর মিলে গিয়েছিল ধৃত সঞ্জয়ের থেকে সংগৃহীত হাতের লেখার নমুনার সঙ্গে।
কেউ কি দেখেছিলেন সেদিন ধৃতদের শ্যামপ্রসাদের বাড়িতে ঢুকতে? রহস্যভেদের পর অনেক খুঁজেছিলেন শুভজিৎ। ঢুকতে দেখেছিলেন, এমন কাউকে পাওয়া না গেলেও খোঁজ মিলেছিল এক স্থানীয় বাসিন্দার। যিনি অরিন্দম ঘোষকে চেনেন দীর্ঘদিন, একই এলাকায় থাকার সুবাদে। পার্ক সাইড রোডের কাছেই কারমেল স্কুল। বিকেলবেলা স্কুলছুটির পর মেয়েকে নিয়ে ফিরছিলেন স্কুটারে করে। পার্ক সাইড রোডের মুখে সাড়ে চারটে-পৌনে পাঁচটা নাগাদ অরিন্দম এবং অন্যদের একটা সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন। পাশে পার্ক করা ছিল সেই কালো স্যান্ট্রো। কৌতূহলবশত জিজ্ঞেস করেছিলেন, ‘কী রে বাবলা, এখানে এখন?’ অরিন্দম বলেছিলেন, ‘এই তো ইভনিং শো-তে মেনকায় সিনেমা দেখতে যাব আজ।’ গুরুত্বপূর্ণ পারিপার্শ্বিক প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল এই সাক্ষ্য। যাতে সঙ্গত করেছিল ধৃত সাতের সেদিনের মোবাইল টাওয়ার লোকেশন, বিকেল পৌনে পাঁচ থেকে সাড়ে ছ’টার।
বিচারপর্বে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন অভিযুক্ত সাতজন। অরিন্দম-অম্লান-সঞ্জয়, অমিত-বিজয় রায়-রাম কুমার-বিজয়বাহাদুর সিং। দণ্ডাদেশ? যাবজ্জীবন কারাবাস। এখনও জেলেই দিনযাপন।
মার্ক টোয়েন লিখেছিলেন, ‘Truth is stranger than fiction, but it is because fiction is obliged to stick to possibilities. Truth isn’t.’
খাঁটি কথা। ‘সত্যি’ সত্যিই হার মানায় বাস্তবকে, ফিকশনকে বলে বলে গোল দিতে পারে কখনওসখনও। কল্পকাহিনির লক্ষ্মণরেখা চিহ্নিত থাকে সম্ভাব্যতার সীমায়। বাস্তবের সে দায় নেই। থাকলে এভাবে প্রাণ যায় শ্যামপ্রসাদের? এভাবে জেলকুঠুরিতে পচতে হয় সাতজনকে? অর্থলিপ্সা ছিল উভয়তই। যিনি খুন হলেন, তাঁর। যারা খুন করেছিল, তাদেরও।
স্নেহ অতি বিষম বস্তু। লোভ বিষমতর।
পুনশ্চ: সাত্যকি মল্লিক এবং সুরজিৎ রায়, এই দুটি নাম পরিবর্তিত। ওঁরা জীবিত। ওঁদের স্বাভাবিক সামাজিক জীবনে এই কেস নিয়ে কৌতূহলী প্রশ্ন আর অহেতুক বিড়ম্বনার আবির্ভাব হোক এত বছর পরে, অভিপ্রেত নয়, তাই।
২.০৯ বিশ্বাসই বিশ্বাসঘাতক
[মঞ্জু ঘোষাল হত্যা
মলয় দত্ত, সাব-ইনস্পেকটর, গোয়েন্দাবিভাগ। ২০১৬ সালে পেয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রদত্ত ‘সেবা পদক’।]
দরজাটা বন্ধ কেন? মঞ্জুদির তো খুলে বেরিয়ে আসার কথা, বেরিয়ে দাঁড়ানোর কথা দরজার মুখে। এমনটাই তো হয়ে আসছে এতদিন ধরে। আজ অন্যথা কেন? কেউ আছে ভিতরে? সামান্য থমকান ডলি। একটু ইতস্তত করেন। বেল বাজান। উত্তর নেই কোনও। সামান্য জোরেই ডাক দেন এবার।
—মঞ্জুদি?
সেকেন্ড পাঁচেক পরেও যখন আওয়াজ নেই কোনও ঘরের ভিতর থেকে, গলা আর একটু চড়ান ডলি।
— মঞ্জুদি.. আমি ডলি। মঞ্জুদি…?
কী হল? এমন তো হওয়ার কথা নয়। মঞ্জুদি সাড়া দিচ্ছে না কেন? শরীরটা ইদানীং ভাল যাচ্ছিল না। মাথা-টাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে গেল? নাকি পেনশন তুলতে বেরিয়েছে? কিন্তু সে তো দিনচারেক আগেই তুলে এনেছে ব্যাংক থেকে। তা ছাড়া বেরলে তো দরজায় তালা দেওয়া থাকবে। নেই তো! উদ্বিগ্ন ডলির কী মনে হয়, দরজায় সামান্য চাপ দিয়ে দেখেন। এবং খুলে যায় অর্ধেকটা, ওই সামান্য চাপেই। দরজাটা খোলাই ছিল, ভেজানো। ডলি দ্বিধা কাটিয়ে ঘরে ঢুকে পড়েন।
ফ্ল্যাটে ঢুকেই সামান্য একচিলতে জায়গা। পেরিয়ে বাঁ দিকে একটা শোওয়ার ঘর। খোলা। কেউ নেই ভিতরে। বিছানাটা ওলটপালট অবস্থায়। জিনিসপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। ভয় পেয়ে যান ডলি। মঞ্জুদি কোথায়?
এ ফ্ল্যাটে সে-অর্থে ড্রয়িংরুমের কোনও বালাই নেই। ডানদিকে একটা ছোট প্যাসেজ। বাথরুম-রান্নাঘর ছাড়া আরেকটা শোওয়ার ঘর। যার দরজাটা একটু খোলা। ডলি ঠেলে খুললেন। এবং খুলেই দাঁড়িয়ে পড়লেন স্থাণুবৎ।
‘মঞ্জুদি’ পড়ে আছেন বিছানায়। উপুড় হয়ে। লাল-সাদা রংয়ের যে নাইটিটা পরে ছিলেন, ভেসে যাচ্ছে রক্তে। শরীরের উপরিভাগ খাটের উপর। হাঁটু থেকে নিম্নাংশ খাটের নীচে। ঝুলছে। ঘর লন্ডভন্ড।
ডলি কাঁপতে থাকেন। ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে কোনওমতে উঠে আসেন তিনতলায়, নিজের ফ্ল্যাটে। হাত চেপে ধরেন স্বামী শেখরের, ‘নীচে চলো… মঞ্জুদি…!’
সত্তর ছুঁইছুঁই শেখর দু’তলায় নামেন যত দ্রুত সম্ভব। দেখেন, এবং বোঝেন, প্রতিবেশীদের বা মৃতা মঞ্জুর আত্মীয়দের খবর দেওয়ার আগেও জরুরি পুলিশকে জানানো। থামান কাঁদতে থাকা ডলিকে।
—ওঁর মেয়েকে ফোন করো। আমি ততক্ষণ থানায় জানাচ্ছি।
সকাল সোয়া এগারোটায় ফোন বাজল কালীঘাট থানায়। ডিউটি অফিসার ধরলেন, শুনলেন, জানালেন ওসি-কে। দুটো ফোন করলেন ওসি। একটা ডিসি সাউথ-কে, আরেকটা ডিসি ডিডি-কে। তারপর গাড়িতে উঠে বসলেন, ড্রাইভারের প্রতি নির্দেশ এল ঝটিতি।
—নেপাল ভট্চাজ স্ট্রিট, তাড়াতাড়ি।
ডিসি সাউথও পার্ক স্ট্রিটের অফিস থেকে রওনা দিলেন। যার কিছু পরেই লালবাজার থেকে স্টার্ট নিল ডিসি ডিডি-র গাড়ি।
গন্তব্য? কোথায় আর, কালীঘাট।
.
ন’বছর আগের মামলা। মঞ্জু ঘোষাল হত্যারহস্য। কালীঘাট থানা, কেস নম্বর ১৮৬, তারিখ ৬ নভেম্বর, ২০০৯। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪/৩৯৪ ধারায়। খুন, একই অপরাধের উদ্দেশ্যে একাধিকের সম্মিলিত পরিকল্পনা এবং লুঠের উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত আঘাত।
১, নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রিট। কালীঘাট থানা থেকে গাড়িতে মিনিট দুই-তিনের দূরত্বে। রাসবিহারী মোড় থেকে পশ্চিমদিকে কিছুটা এগিয়েই ডান হাতে পড়বে সদানন্দ রোড। সেই রাস্তা ধরে সামান্য এগিয়েই বাঁ দিকে পাবেন নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রিট। বাদামতলা আষাঢ় সংঘের পুজোটা যে জায়গায় হয়, তার দশ-বিশ মিটারের মধ্যেই অকুস্থল।
একই ঠিকানাতে দুটো বাড়ি পাশাপাশি। দুটোই চারতলা। বাড়ি দুটোতে ভাড়াটিয়া হিসেবে ৩২টি পরিবারের বাস। একটাই বড় গেট ঢোকার।
মঞ্জু ঘোষাল যে ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকতেন, সেটা দোতলায়। মঞ্জু এবং তাঁর স্বামী নারায়ণচন্দ্র ঘোষাল, দু’জনেই ডাক ও তার বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। নারায়ণবাবু আটের দশকের শেষাশেষি চাকরি থেকে অবসর নেন। মঞ্জুও শারীরিক অসুস্থতার কারণে স্বেচ্ছাবসর নিয়েছিলেন ২০০৫ সালে।
ঘোষাল দম্পতির একমাত্র সন্তান, মানসী। ডাক নাম বুলা। সম্বন্ধ করে মানসীর বিয়ে হয়েছিল ১৯৯৯-তে। সিঁথির বাসিন্দা দীপঙ্কর মিত্রের সঙ্গে। মানসী-দীপঙ্করের বিয়ের মাস দেড়েকের মধ্যেই মৃত্যু হয় নারায়ণবাবুর। সেই থেকে মঞ্জু একাই থাকতেন দোতলার ওই ফ্ল্যাটে। যেখানে দিনদুপুরে কে বা কারা এসে কুপিয়ে খুন করে গেল ষাট বছরের প্রৌঢ়াকে।
কৌতূহলী প্রতিবেশীদের ভিড় সরিয়ে ফ্ল্যাট সম্পূর্ণ খালি করে দিয়ে যা যা নজরে এল পুলিশের, জানানো যাক। মঞ্জু রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে ছিলেন উপুড় হয়ে। চিত করে দিয়ে দেখা গেল, গালে ছড়ে যাওয়ার দাগ। শরীরের দু’জায়গায় ধারালো অস্ত্রের আঘাত। গলার নলি কাটা। রক্ত ঝরেছে প্রচুর। দ্বিতীয় ক্ষতচিহ্ন পেটে। ছুরি হোক বা ধারালো অন্য কিছু, আততায়ী বা আততায়ীরা সোজা ঢুকিয়ে দিয়েছিল পেটে। নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছে। লাল-সাদা নাইটিটা রক্তধারায় প্রায় পুরোটাই লাল। সাদা রং খুঁজতে দূরবিন লাগবে।
মেঝেতে পড়ে প্লাস্টিকের চপ্পল একজোড়া, দৃশ্যতই মঞ্জুর রোজকার ব্যবহারের। চশমাটা পড়ে বিছানায়, বালিশের পাশে। বাড়ির ল্যান্ডফোনের রিসিভারটা মাটিতে পড়ে, তার ছেঁড়া। দুটো শোওয়ার ঘরই তছনছ অবস্থায়। বালিশ-বিছানা, আলনায় রাখা কাপড়চোপড়, প্লাস্টিকের ছোটখাটো ব্যাগ, কিছুই বাদ দেয়নি খুনি বা খুনিরা। হাতড়েছে সব।
যে বিছানায় মঞ্জুদেবীর মৃতদেহ পড়ে ছিল, তার পাশে স্টিলের আলমারি একটা। বন্ধ, কিন্তু চাবি ঘোরানোর জায়গায় একাধিক ‘টুলমার্ক’। চাবি না পেয়ে কোনও যন্ত্রপাতি দিয়ে খোলার চেষ্টা করলে যেমন দাগ হয়। খুনের পর যে ফ্ল্যাটের যেখানে যা টাকাপয়সা-গয়নাগাটি আছে, হাতানোর মরিয়া চেষ্টা হয়েছিল, বুঝতে ফেলুদা বা ব্যোমকেশ হওয়ার দরকার নেই। ঝলকের দেখাই যথেষ্ট।
মঞ্জুর মৃতদেহ উদ্ধার হল যে ঘরে, সে ঘরেই একটা মাঝারি সাইজ়ের ডাইনিং টেবিল। যার উপর দুটো চায়ের কাপ। একটা স্টিলের, আরেকটা পোর্সেলিনের। চায়ের তলানি পড়ে আছে দুটো কাপেই। আর একটা বড় চায়ের কাপ পড়ে আছে মেঝেতে। হ্যান্ডলটা ভেঙে গেছে, পড়ে আছে কাপের পাশে। একটা নিশ্চয়ই মঞ্জুর, অন্য দুটো? খুনি এক নয়, দু’জন?
বাথরুমের ভিতরটা দেখা হল। অস্বাভাবিক কিছু নেই। দেখা হল রান্নাঘরও। সিঙ্কে কিছু থালাবাসন পড়ে আছে। কাপ-প্লেট-বাটি-চামচ-বয়াম রাখা আছে কিচেনের তাকে, যেমন থাকে যে-কোনও মধ্যবিত্ত বাড়িতে। সবজি পড়ে আছে ঝুড়িভরতি।
ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা ঘুরে দেখলেন ফ্ল্যাটের প্রতিটি ইঞ্চি-সেন্টিমিটার-মিলিমিটার। আঙুলের ছাপ পাওয়া গেল দুটো জায়গায়। স্টিলের আলমারিতে, আর ডাইনিং টেবিলের উপর রাখা দুটো চায়ের কাপে। তৈরি হল ‘seizure list’, বাজেয়াপ্ত করা জিনিসের তালিকায় থাকল মঞ্জুদেবীর বিছানায় লাগা রক্তের ছোপের নমুনা, রক্তমাখা বিছানার চাদর ও বালিশের কভার, নীল রংয়ের একটা ক্যারিব্যাগ রক্তমাখা, আঙুলের ছাপ সহ দুটো চায়ের কাপ, মাটিতে পড়ে থাকা কাপ এবং তার ভাঙা হ্যান্ডল।
ততক্ষণে এসে পৌঁছেছে গোয়েন্দাবিভাগের CD Van (Corpse Disposal), বিশেষ শববাহী গাড়ি। ময়নাতদন্তে পাঠানোর জন্য যখন নীচে নামানো হচ্ছে মঞ্জুদেবীর নিথর দেহ, স্থানীয় মানুষের ভিড়ে থিকথিক নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রিট। গাড়িতে তুলে ‘বডি’ বার করতেই কালঘাম ছুটে গেল পুলিশের। ডিসি সাউথ আর ডিসি ডিডি নীচে নামতেই ধেয়ে এল ইলেকট্রনিক মিডিয়ার কয়েক ডজন বুম।
—খুনের কারণ কিছু জানা গেল?
—আপনারা কি পরিচিত কাউকে সন্দেহ করছেন?
—সকালবেলা এভাবে একজন বয়স্ক মহিলা খুন হয়ে গেলেন, এটা কি শহরে নাগরিকদের নিরাপত্তা রক্ষায় কলকাতা পুলিশের ব্যর্থতা নয়?
—ফরেনসিক এক্সপার্টরা কী বললেন?
—সিপি কি স্পট ভিজিটে আসবেন?
প্রশ্ন ঝাঁকে ঝাঁকে। একে অন্যকে শেষ করার সুযোগ না দিয়েই। ডিসি ডিডি শান্ত ভাবে বললেন, ‘তদন্ত সবে শুরু হয়েছে। খুনের কিনারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব করার চেষ্টা করব আমরা। সমস্ত সম্ভাবনাই খতিয়ে দেখা হবে।’
ডিসি সাউথ যোগ করলেন, ‘একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে। খুবই দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে শহরের নাগরিকদের নিরাপত্তায় কলকাতা পুলিশ ব্যর্থ, এই ধারণা করা অতি সরলীকরণ হবে বলে আমাদের মনে হয়।’
এটুকুই যথেষ্ট ছিল। শুরু হয়ে যায় ‘লাইভ’ সম্প্রচার, কালীঘাট থেকে অমুকের সঙ্গে ক্যামেরায় তমুক।
‘আপনারা শুনলেন, কালীঘাটে প্রৌঢ়ার নৃশংস খুনকে স্রেফ ‘বিচ্ছিন্ন ঘটনা’ বলে দায় এড়ালেন ডিসি সাউথ। কিন্তু স্থানীয় মানুষ এই ঘটনায় চূড়ান্ত আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন শহরের বয়স্কদের নিরাপত্তা নিয়ে। থানার এত কাছে দিনদুপুরে ঘটে যাওয়া এই খুনে প্রশ্ন উঠছে কালীঘাট থানার ভূমিকা নিয়েও। আমরা এখন শুনে নেব, স্থানীয় বাসিন্দারা ঠিক কতটা আতঙ্কগ্রস্ত… আচ্ছা…আপনি তো এখানেই থাকেন… এভাবে দিনের বেলায় এই নৃশংস খুন…’
মিডিয়া মিডিয়ার কাজ করছিল। পুলিশ পুলিশের। যখন ফ্ল্যাটের ভিতরটা সরেজমিনে দেখছিলেন পুলিশকর্তারা-ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা, প্রাথমিক বিবরণ ফোনে শুনে নিয়েই সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছিলেন নগরপাল। কেসটা ডিডি করবে। তদন্তের দায়িত্ব পড়েছিল হোমিসাইড শাখার তরুণ সাব-ইনস্পেকটর মলয়কুমার দত্তর উপর।
.
তথ্যসংগ্রহের প্রাথমিক কাজকর্ম সেরে মলয় যখন বেরলেন বাড়ি ফেরার জন্য, রাত সাড়ে ন’টা বেজে গেছে প্রায়। তিন-চারটে তো নয়, ৩২টা ফ্ল্যাট। সব মিলিয়ে একশোর উপর বাসিন্দা। প্রত্যেকের ঠিকুজিকুষ্ঠি জোগাড় করতেই তো ঘণ্টা তিনেক চলে গেল। তা-ও শেষ হয়নি পুরোটা। বাকি আছে আরও। কে কী করেন, ঘটনার সময় কোথায় ছিলেন, কার মোবাইল নম্বর কত, খুঁটিয়ে জানতে আরও একটা দিন লাগবে।
তবে দিন একেবারে নিষ্ফলাও যায়নি। খুনটা যে পরিচিত বা পরিচিতরাই করেছে, এবং উদ্দেশ্য যে ছিল টাকাপয়সা-গয়নাগাটি লুঠপাট, সেটা মোটামুটি ধরা যেতেই পারে। এখনও ‘মোটামুটি’, কারণ এক শতাংশ সম্ভাবনা এসব ক্ষেত্রে থাকেই, খুনটা হল সম্পূর্ণ অন্য কারণে, কিন্তু পুলিশকে ‘মিসলিড’ করতে চেহারা দেওয়া হল লুঠপাটের। তেমন কিছু তো এখনও মনে হচ্ছে না, ফিরতে ফিরতে ভাবেন মলয়। যা যা জানা গেল আজ দিনভর জিজ্ঞাসাবাদে, মনে মনে ঝালিয়ে নেন একবার।
ডলি রায়, যিনি আবিষ্কার করেন মৃতদেহ, মঞ্জুর ঘনিষ্ঠতম প্রতিবেশিনী ছিলেন। দু’জনে ছিলেন প্রায় সমবয়সিই। এতটাই ঘনিষ্ঠ ছিলেন দু’জনে, যে দুই পরিবারের নিজেদের মধ্যে যোগাযোগের জন্য আলাদা কলিংবেল ছিল দুটো ফ্ল্যাটেই। আলাদা বেল, আলাদা আওয়াজ।
মঞ্জু বছর পাঁচেক ধরে নানা রোগে ভুগছিলেন। ব্লাডপ্রেসারের দোসর হয়েছিল ব্লাডসুগার। বছরখানেক হল ব্যাধির তালিকায় নতুন সংযোজন হয়েছিল আর্থারাইটিস। হাঁটুর ব্যথায় কাবু হয়ে থাকতেন বছরভর।
বাড়ির বাইরে বেরতেন মাসে একবারই। রিকশা করে ব্যাংকে যেতেন পেনশনের টাকা তুলতে। ব্যস, ওই একবারই। বাকি সময় ঘরেই। মাসকাবারি বাজার করে দিয়ে যেতেন মেয়ে মানসী বা জামাই দীপঙ্কর। রোজকার বাজারহাট আর টুকটাক কেনাকাটা, যখন প্রয়োজন হত, করে দিতেন প্রতিবেশীরাই। দিনে অন্তত দু’বার ডলি নিয়ম করে মঞ্জুর ফ্ল্যাটে আসতেন। ডলির থেকে আরও জানা গেল, মঞ্জু বাড়িতে সবসময় গলায় সোনার চেন পরে থাকতেন। আর হাতে সোনার চুড়ি। যা পাওয়া যায়নি মৃতদেহে। নিয়ে গেছে আততায়ীরা।
—কিছু দরকার হলে, বা এমনিই গল্প করার ইচ্ছে হলে মঞ্জুদি কলিংবেল বাজাত আমাদের ফ্ল্যাটে। যখন আমার যাওয়ার হত মঞ্জুদির ফ্ল্যাটে, আমিও বেল বাজাতাম উপর থেকে। মঞ্জুদি দরজা খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত দরজার মুখটায়। অপরিচিত কাউকে এমনিতে দরজা খুলতই না। ভিতর থেকে হাঁক দিয়ে জিজ্ঞেস করত, ‘কে? কী দরকার?’ চেনা কেউ এসেছে, একশোভাগ নিশ্চিত হয়ে তবেই খুলত।
—আজও উপর থেকে বেল বাজিয়ে নীচে এসেছিলেন?
—হ্যাঁ, ওটা অভ্যেস হয়ে গেছে আমাদের। মঞ্জুদির হাঁটুর ব্যথা শুরু হওয়ার পর থেকেই ওই ব্যবস্থা। রোজ সকালে এগারোটা নাগাদ নীচে আসতাম জর্দা আর সেদিনের ‘আনন্দবাজার’ কাগজটা নিয়ে। আজও বেল বাজালাম। নীচে এলাম, দেখি দরজা বন্ধ। ডাকলাম, সাড়া দিল না। দরজা ঠেললাম একটু পরে। খুলে গেল। ঢুকে দেখি এই কাণ্ড….।
হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেন ডলি।
আতঙ্কের ঘোর কাটার পর স্বামী শেখরকে উপর থেকে ডেকে এনেছিলেন ডলি। শেখর রায়, বয়স সত্তরের উপর। রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী। শেখর স্নেহ করতেন মঞ্জুকে, ডাকতেন ‘মা’ বলে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এমন কোনও তথ্য পাওয়া গেল না, যা ডলি জানাননি পুলিশকে।
ডলি-শেখরের একমাত্র সন্তান সুমিত। বয়স সবে চল্লিশ পেরিয়েছে। অবিবাহিত। নেপাল ভট্টাচার্য লেনেই একটা ট্র্যাভেল এজেন্সির অফিস চালান। সুমিত রায়ের বয়ান অনুযায়ী, পৌনে দশটা নাগাদ রোজকার মতো অফিসে বেরিয়েছিলেন পায়ে হেঁটে। সাড়ে এগারোটা নাগাদ বাড়ি থেকে ফোন পান, মঞ্জুদেবী খুন হয়ে গেছেন। তড়িঘড়ি ফিরে আসেন।
আর একটি তথ্য দিলেন সুমিত। আন্দাজ সাড়ে ন’টা নাগাদ এক যুবক বেল বাজিয়েছিল তাঁদের তিনতলার ফ্ল্যাটে। বলেছিল, আনন্দবাজার পত্রিকার মার্কেটিং বিভাগের কর্মী। আনন্দবাজার এবং টেলিগ্রাফের দৈনিক গ্রাহক হওয়ার ‘কম্বো অফার’ নিতে আগ্রহী কিনা, জানতে চেয়েছিল। সুমিত আগ্রহ দেখাননি। যুবক উঠে গিয়েছিল চারতলায়।
চারতলায় কোথায় গিয়েছিল? ভরদ্বাজ পরিবারের ফ্ল্যাটে। স্ত্রী-কন্যা নিয়ে দীর্ঘদিন এই ফ্ল্যাটে ভাড়া থাকেন ওমপ্রকাশ ভরদ্বাজ। ব্যবসা করেন। স্ত্রীর নাম মধুবালা। একমাত্র কন্যা প্রীতির বয়স একুশ। কস্টিং পড়ার পাশাপাশি চাকরি করেন সল্টলেকের একটি বিপিও-তে। প্রীতি জানালেন, আনন্দবাজারের ওই কর্মী তাঁদের ফ্ল্যাটেও গিয়েছিল। ‘কম্বো অফার’ নিতে রাজি হয়েছিলেন প্রীতিরা। ফর্মে সই করে রিসিট দিয়ে গেছে যুবকটি। নিজের নাম আর ফোন নম্বরও লিখে দিয়েছে রিসিটের পিছনে। কী নাম? শুভঙ্কর দে।
ফোনে সঙ্গে সঙ্গেই শুভঙ্করকে ধরেছিলেন মলয়। বিকেল চারটে নাগাদ। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যেই আনন্দবাজারের প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিটের অফিস থেকে কালীঘাটে চলে এসেছিলেন বাইশ বছরের শুভঙ্কর। মিনিট পনেরো কথা বলেই মলয় বুঝেছিলেন, ছেলেটি সত্যিই মার্কেটিং-এর কাজে এসেছিল। কোথাও কোনও গণ্ডগোল নেই। একটাই জিনিস শুধু জানার ছিল।
—যখন উঠছেন সিঁড়ি দিয়ে, বা নেমে আসছেন, কাউকে উঠতে বা নেমে যেতে দেখেছিলেন? মনে করে দেখুন…।
একটু ভাবেন শুভঙ্কর।
—না স্যার, অত খেয়াল করিনি। আমি ফোনে কয়েকটা এসএমএস চেক করতে করতে উঠছিলাম। খেয়াল করিনি।
—তবু মনে করে দেখুন না একটু…
শুভঙ্কর হাসেন।
—ভাল করে দেখলে তবে তো মনে থাকবে। দেখিইনি তো খেয়াল করে। এখন কিছু বলতে গেলে বানিয়ে বলতে হবে স্যার।
সূত্রের খোঁজে মরিয়া মলয় তবু প্রশ্ন করেন।
—যখন দোতলা থেকে তিনতলায় উঠছেন, দোতলার দরজা খোলা ছিল?
—না, বন্ধ ছিল। আমি তো দোতলাতেও বেল বাজিয়েছিলাম। মিনিট খানেক অপেক্ষা করেছিলাম। কেউ খোলেনি দরজা। তারপর তিনতলায় উঠে গিয়েছিলাম।
—সময় তখন আন্দাজ ক’টা হবে?
—এই সাড়ে ন’টার আশেপাশে হবে।
—যখন নেমে আসছিলেন, তখনও বন্ধ ছিল দোতলার দরজা?
শুভঙ্কর সামান্য হেসে ফেলেন এবার।
—খেয়াল করিনি এত স্যার।
এঁকে আর জিজ্ঞাসা করে নতুন কিছু পাওয়ার নেই। বরং জানা দরকার, কার কার রোজ মঞ্জুদেবীর ঘরে ঢোকার প্রবেশাধিকার ছিল। উত্তর পাওয়া গেল মানসী মৈত্রর কাছে। মৃতার একমাত্র সন্তান। যিনি কেঁদেই চলেছেন মায়ের ফ্ল্যাটে চলে আসার পর থেকে। সান্ত্বনা দিতে ব্যর্থ হচ্ছেন স্বামী দীপঙ্কর।
কান্নাভেজা গলায় যতটুকু বললেন সদ্য মাতৃহারা মানসী, মোটামুটি এই।
—মা একা থাকত বলে খুব সতর্ক ছিল অচেনা লোককে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়ার ব্যাপারে। আমিও মা-কে সাবধান করতাম নিয়মিত। একা মানুষ থাকে। কখন কী হয় বলা যায়?
—ওঁর বাজারহাট-টাট… এসব কি আপনিই…
—হ্যাঁ, সপ্তাহে একবার আমি এসে করে দিয়ে যেতাম। আমি না পারলে আমার স্বামী আসতেন। সপ্তাহের বাজার, ওষুধপত্র, এই সব। বাকি ডলি কাকিমারা দেখে নিতেন হঠাৎ কিছু দরকার হলে। আর উষাদি তো ছিলই।
‘উষাদি’ বলতে ‘উষারানি দেবী’। আটপৌরে মলিন শাড়ির পঞ্চাশোর্ধ্বা মহিলা, যিনি ফ্ল্যাটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন ঠায়। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেই চলেছেন। উষারানি এ বাড়িতে ঠিকের কাজ করছেন প্রায় বছর দশেক হল। এই আবাসনের আরও তিনটে ফ্ল্যাটেও কাজ করেন। বাড়ি ক্যানিংয়ে। রোজ সকালের ট্রেনে আসেন কলকাতায়। মঞ্জুর ফ্ল্যাটে সাতটা-সাড়ে সাতটায় ঢুকে ঝাড়পোঁছ করে অন্য ফ্ল্যাটগুলোর কাজ সারেন। দুপুরে ফের মঞ্জুর ফ্ল্যাটে চলে এসে কাপড় কাচা, বাসন মাজা, একটু রান্নাবান্না, টুকটাক ফাইফরমাশ খাটা, এবং বিকেলের ট্রেনে বাড়ি ফেরা। মঞ্জুর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেই ডুকরে কেঁদে ওঠেন।
—‘মা’ আমাকে মেয়ের মতই ভালবাসতেন…
—আর কে আসত? কাজের লোক আর কেউ ছিল?
—হ্যাঁ স্যার, জগদীশ।
—কে জগদীশ?
জগদীশ যাদব। সুইপার, তিরিশ বছর বয়স। রোজ আটটার মধ্যে চলে এসে সাফসুতরো করে যেতেন বাথরুম। তারপর যেতেন আরও কয়েকটা ফ্ল্যাটে।
জগদীশ থাকেন কাছেই, চেতলার লকগেটের কাছে। বাড়িতেই ছিলেন। খবর পাঠাতেই এলেন শক্তপোক্ত চেহারার যুবক। কালো গেঞ্জি আর নীলরঙা বারমুডা পরিহিত জগদীশ জানালেন, যতক্ষণ ছিলেন মঞ্জুর ফ্ল্যাটে, অস্বাভাবিক কিছু দেখেননি।
—আমি আটটায় ঢুকেছিলাম রোজকার মতো। বেরিয়েছিলাম সোয়া আটটা নাগাদ। উষাদি তখন ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল।
মলয় তাকান উষার দিকে। উষা ঘাড় নাড়েন, জগদীশ মিথ্যে বলছে না। আরও দুটো প্রশ্ন ছিল মলয়ের।
—অন্য ফ্ল্যাটগুলোর কাজ সেরে কখন বেরিয়েছিলেন?
—এই স্যার, দশটার কাছাকাছি হবে। পাঁচ-দশ মিনিট এদিক-ওদিক হতে পারে।
—হুঁ, বাড়ি কোথায় আপনার?
—বিহার স্যার। ছাপড়া। বছর সাতেক আগে কলকাতায় এসেছি পেট চালাতে।
এতগুলো ফ্ল্যাট, বাসিন্দাদের সবার ব্যাপারে বিস্তারিত খোঁজখবর নিতেই কেটে গেল আরও দিনদুয়েক। স্বাভাবিক নিয়মে ওই চারতলা বাড়িতে কার কখন প্রবেশাধিকার ছিল, জানা জরুরি ছিল। কোন ফ্ল্যাটে কে কাগজ দিত, কোন ফ্ল্যাটে কে সুইপারের কাজ করত, ঠিকে কাজের লোক কে ছিল কাদের বাড়িতে, কোন দুধওয়ালা সকালে আসত দুধ দিতে, কেবল অপারেটর কারা কারা আসত ফ্ল্যাটবাড়িতে, এই সব।
তথ্য সংগ্রহের এই কাজটা যে কী পরিমাণে ‘শুষ্কং কাষ্ঠং’ হতে পারে, সেটা তদন্তকারী অফিসার মাত্রই জানেন হাড়েহাড়ে। অপরাধটা করেছে হয়তো এক বা দু’জন বা তিন। তদন্তের চূড়ান্ত পর্বে হয়তো সন্দেহভাজনের সংখ্যা দাঁড়াবে বড়জোর পাঁচ কিংবা ছয়ে, তবু কমপক্ষে পঞ্চাশ-ষাট জনকে একই প্রশ্ন করে যেতে হয়। যাঁকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, তাঁর খুনের সঙ্গে কোনও যোগ থাকার সম্ভাবনা শূন্য, এটা জেনেও। এটা জেনেও, বাড়তি কোনও তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনাও হয়তো শূন্যেরই কাছাকাছি।
উদ্দেশ্য একটাই। ‘Process of elimination’, দুধের থেকে জলটা আলাদা করা। অপ্রয়োজনীয় তথ্য একটা একটা করে ছেঁটে ফেলা। মাঠটাকে ছোট করে আনা।
এই আলাদা করার প্রক্রিয়ায় বিস্তর খাটাখাটনি করলেন মলয়। একতলায়, গেট দিয়ে ঠিক ঢোকার মুখে ‘ইলেকট্রোক্রাফট’ বলে একটা দোকান ছিল। ইলেকট্রিক্যাল সরঞ্জামের যে দোকান রোজ সকাল সাড়ে আটটায় ঝাঁপি খুলত, সেই দোকানের সমস্ত কর্মচারীর সঙ্গে কথা বললেন মলয়। পাশেই পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান ছিল একটা। সেখানেও তথ্যতালাশ। রোজকার চেনামুখের বাইরে অন্য কাউকে ঢুকতে দেখছিলেন? কেউই মনে করতে পারলেন না বলার মতো কিছু।
কী করেই বা পারবেন? ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বলছে, খুনটা হয়েছে ন’টা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে। এমন একটা সময়ে, যখন বাসিন্দারা কাজে বেরচ্ছেন একের পর এক। কাজের লোকদের যাতায়াতও লেগেই আছে। রোজকার সকাল-সন্ধে-দুপুর-বিকেল কে আর অত মনে রাখে আলাদা করে, কে-ই বা খেয়াল করে খুঁটিয়ে?
.
—কী দাঁড়াচ্ছে তা হলে?
মলয়কে প্রশ্ন করেন ওসি হোমিসাইড। লালবাজারের গোয়েন্দাবিভাগে পর্যালোচনা চলছে মামলার অগ্রগতির। দিন সাতেক পেরিয়ে গেছে খুনের পর। ‘ক্লু’ বা ‘লিড’ এখনও অধরা।
—স্যার, পসিবল সাসপেক্টদের একটা লিস্ট করেছি। তবে এর বাইরেও হতে পারে অন্য কেউ।
—শুনি।
—এক নম্বরে সুমিত রায়। ডলি-শেখরের ছেলে। আমি খোঁজ নিয়েছি স্যার। ওই ট্রাভেল এজেন্সির ব্যবসা মোটেই ভাল চলছিল না। টাকার দরকার ছিলই।
—‘মোটিভ’ বুঝলাম, কিন্তু ‘অ্যালিবাই’?
—আছে, তবে দুর্ভেদ্য কিছু নয়। বলেছেন, পৌনে দশটা নাগাদ অফিস গেছিলেন। সেটা সত্যিই বলেছেন, ভেরিফাই করেছি। কিন্তু সময়টা ভাবুন স্যার। খুনটা হয়েছে সকাল ন’টা থেকে সাড়ে দশটার মধ্যে। সুমিতবাবু অফিস যাওয়ার পথে কাজটা করে রোজকার মতো বেরিয়ে গেছেন, একেবারে অসম্ভব নয়।
—অসম্ভব নয়….
—আরও একটা জিনিস স্যার, খুনটা যে পরিচিত কেউ করেছে এটা তো পরিষ্কার। যদি দুটো চায়ের কাপ থেকে ধরে নিই, আততায়ী দু’জন ছিল, তা হলেও দু’জনের একজনকে পরিচিত হতেই হবে। না হলে দরজা খুলতেন না মঞ্জুদেবী।
—বুঝলাম, কিন্তু…
—বলছি স্যার। একটা ব্যাপার মাথায় রাখা দরকার, ডলির ফ্ল্যাটের আলাদা কলিংবেলটা, যা দিয়ে মঞ্জুর ফ্ল্যাটের বেল বাজানো যায়, সেটা কিন্তু ইচ্ছে করলেই সুমিতও বাজাতে পারতেন। অ্যাকসেস ছিল।
—হুঁ!
—ধরুন স্যার, উনি বেলটা বাজালেন অফিস বেরনোর আগে। মঞ্জু এসে দাঁড়ালেন দরজার বাইরে। অন্য কাউকে, সে ফ্ল্যাটেরই হোক বা অন্য কোনও লোক, হয়তো আগে থেকে সুমিত বলে রেখেছিলেন। সে-ও ওই সময়ে ঢুকল বাড়িতে। উঠল দোতলায়। সুমিত নেমে এলেন। মঞ্জুকে হয়তো কোনও দরকারি কথার ব্যাপারে বললেন। সঙ্গের বন্ধুকেও ডেকে নিলেন, চা খাওয়ার পর দু’জনে মিলে খুনটা করলেন।
—থিয়োরেটিকালি অসম্ভব নয়, প্র্যাকটিক্যালিও হয়তো নয়, হতেই পারে। আর, সুমিত এবং তার সঙ্গী করেছে বলে ধরে নেওয়াটাও ঠিক নয়, হয়তো করিয়েছে। ভাড়াটে লোক দিয়ে। যারা অপেক্ষায় ছিল নীচে। নির্দিষ্ট সময় বলা ছিল। যারা সময়মতো উঠে এসে বেল বাজিয়েছে। আর মঞ্জু কিছু বোঝার আগেই সুমিত ভিতর থেকে খুলে দিয়েছেন দরজা, এবং খুলে দিয়ে বেরিয়ে গেছেন সঙ্গীকে নিয়ে, ভাড়াটে খুনিরা ‘অ্যাকশন’ করে বেরিয়ে গেছে।
—পসিবল স্যার…
—কিন্তু সুমিতই হোক বা অন্য কেউ, লাভ তো কিছু হল না। ওই তো কয়েকটা গয়না, যা পরে থাকতেন। বেচে বড়জোর দশ হাজার। আর ব্যাগে ট্যাগে হয়তো কিছু টাকা ছিল। সেটা নিয়ে গেছে। কতই বা হবে? হাজার দুই-তিন খুব বেশি হলে। তার বেশি টাকা তো বাইরে থাকার কথা নয়।
—সেটা অপরাধীদের ব্যাড লাক স্যার। ভদ্রমহিলা এবং ওঁর স্বামী, দু’জনেই সরকারি চাকরি করেছেন দীর্ঘদিন। টাকাপয়সার অভাব ছিল না। যে কেউ ভাববে, আলমারি ভাঙতে পারলে ভালই আমদানি হবে। আলমারির চাবি মঞ্জু রাখতেন রান্নাঘরে একটা শিশির মধ্যে। ওটা খুঁজে পায়নি খুনিরা।
—হুঁ।
—সাসপেক্ট নাম্বার টু, জগদীশ। সুইপার। পেটানো চেহারা।
ওসি হোমিসাইড হেসে ফেলেন।
—মলয়, চেহারা গুন্ডার মতো হলেই যে গুন্ডা হতে হবে, এমন কথা নেই কিন্তু।
মলয়ও মৃদু হেসেই উত্তর দেন।
—সে তো জানি স্যার। কিন্তু এর ক্ষেত্রেও ওই ফ্যাক্টর দুটো অ্যাপ্লিকেবল। টাকা এবং পরিচিত হিসেবে প্রবেশাধিকার।
—কিন্তু উষা তো বলছেন, কাজ সেরে বেরিয়ে গিয়েছিল জগদীশ!
—উষা বেরিয়ে যাওয়ার পর ফিরে আসেনি কাউকে নিয়ে, কী গ্যারান্টি আছে?
—হ্যাঁ, কিন্তু সুইপারকে ডাইনিং টেবিলে বসিয়ে চা খাওয়ায় কেউ?
—রাইট স্যার, ওখানেই খটকা।
—ব্যাক গ্রাউন্ড চেক করেছ জগদীশের?
—করেছি স্যার। বলার মতো কিছু পাইনি। রাত্রে মদ-টদ খায়, এই পর্যন্ত। ক্রিমিনাল রেকর্ড কিছু নেই। লোক লাগানো আছে। টাকা ওড়াচ্ছে কিনা, খবর রাখতে বলেছি।
ওসি হোমিসাইড বুঝতে পারেন দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায়, মলয় দিনরাত খাটছে ঠিকই, কিন্তু তদন্ত এখনও ঘুরপাক খাচ্ছে সম্ভাব্যতার গণ্ডিতে। নির্দিষ্ট ‘ক্লু’ এখনও নেই। নেই প্রমাণ।
—আর কোনও সাসপেক্ট?
—সে-অর্থে সাসপেক্ট বলব না স্যার, কিন্তু মঞ্জুদেবীর জামাই দীপঙ্করের আর্থিক অবস্থাও যে খুব ভাল ছিল এমন নয়। আরও খোঁজ নিচ্ছি স্যার। ক্লিন চিট দেওয়ার জায়গায় কেউই নেই।
—গুড। আমরা যখন ট্রেনিং-এ ছিলাম, কী বলা হত জানো? তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে কাউকে বিশ্বাস করতে নেই। ‘Believe nobody, trust nobody’। সব কিছু বারবার যাচাই করে তবেই বিশ্বাসের প্রশ্ন, সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার প্রশ্ন। সে যে-ই হোক না কেন। মৃতের মা-বাবাই হোক বা স্ত্রী-পুত্র, বা মেয়ে-জামাই। আচ্ছা, হোয়াট অ্যাবাউট ভরদ্বাজ ফ্যামিলি? যারা চারতলায় থাকত?
—মিস্টার ভরদ্বাজের ব্যবসা সংক্রান্ত কোনও আর্থিক সমস্যা ছিল না। মধুবালার সঙ্গে, আই মিন মিসেস ভরদ্বাজের সঙ্গে মঞ্জুদেবীর সুসম্পর্ক ছিল। ওঁদের মেয়ে প্রীতিকে মঞ্জু খুবই ভালবাসতেন। প্রতি পুজোয় জামাকাপড় কিনে দিতেন। ঘটনার সঙ্গে এই ফ্যামিলির কোনওরকম ইনভলভমেন্টের সম্ভাবনা দেখছি না। অন্তত এখনও পর্যন্ত।
—বেশ …
—রইল বাকি উষারানি। ট্র্যাক রাখছি মহিলার। মঞ্জুদেবীর মেয়ে মানসীকে আলাদা করে জিজ্ঞেস করেছি উষারানির ব্যাপারে।
—কী বললেন?
—বললেন, ‘উষাদিকে দশ বছর ধরে দেখছি। নিজের মায়ের মতো ভালবাসত মা-কে। আমাকে ভালবাসে মেয়ের মতো। এর সঙ্গে উষাদি জড়িত, দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারি না। উষাদি আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে গেছিলেন।’
—হুঁ… উষার বাড়িতে কে কে আছেন?
—স্বামী মারা গেছেন। একা থাকেন ক্যানিং-এ। এক মেয়ে। বিয়ে হয়ে গেছে। মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে তেমন যোগাযোগ নেই।
—সোর্সকে তবু বলে রেখো।
—বলেছি স্যার। এমন তো কতই হয়, দীর্ঘদিনের কাজের লোক বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে বাইরে কাউকে খবর দিয়ে দিল…
—হ্যাঁ, ভেরি কমন। ট্র্যাক রাখো।
—ইয়েস স্যার।
মলয় উঠে পড়ার মুখে থামান ওসি হোমিসাইড।
—আর হ্যাঁ, ইলেকট্রনিক সারভেল্যান্স…কাউকে বাদ দিয়ো না কিন্তু… সে যে-ই হোক… কাউকেই না…
—ওটা চলছে স্যার। ফ্ল্যাটের সমস্ত বাসিন্দাদের কল ডিটেল রেকর্ডস চেয়েছি। কে কার সঙ্গে কখন কথা বলেছে বা বলছে, আপডেট রাখছি।
.
পরের দিন বিকেল। হন্তদন্ত হয়ে মলয় ঘরে ঢুকলেন গোয়েন্দাপ্রধানের। হাতে ‘কল ডিটেলস’-এর শিট একটা।
—স্যার, এই দেখুন!
—কী হল মলয়?
মলয় ‘কল ডিটেলস’-এর একটা পাতা মেলে ধরেন।
—গত রাতে সুমিত রায় একজন অ্যাডভোকেটের সঙ্গে কথা বলেছে। মোস্ট প্রবাবলি অ্যান্টিসিপেটরি বেল মুভ করবে কাল-পরশুর মধ্যে।
গোয়েন্দাপ্রধান নড়েচড়ে বসেন।
—কী করে বুঝছ, অ্যান্টিসিপেটরি বেল মুভ করবে?
—অ্যাডভোকেটের নম্বর তো কল রেকর্ডসেই আছে। একটু আগে ফোনে কথা বললাম ওঁর সঙ্গে। আলিপুর কোর্টে প্র্যাকটিস করেন। উনিই বললেন।
—হুঁ, সুমিতকে নিয়ে এসো লালবাজারে। এখনই।
—রাইট স্যার।
‘ইন্টারোগেশন রুম’ বলতে সাধারণত যে ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে, একটা আধো-অন্ধকার ঘর। সিলিং থেকে অল্প পাওয়ারের একটা বালব ঝুলছে। গা-ছমছমে একটা পরিবেশে সন্দেহভাজনকে হাড়হিমকরা গলায় জেরা করছেন অফিসার।
লালবাজারের ‘ইন্টারোগেশন রুম’-এ ওই ‘সিনেমায় যেমন হয়’ জাতীয় ব্যাপারই নেই কোনও। সাদামাটা ঘর, খুব বেশি হলে আট ফুট বাই ছয়। একটা টেবিল, যার দু’দিকে দুটো চেয়ার পাতার মতোই জায়গা আছে শুধু। একটায় তদন্তকারী অফিসার বসেন। উলটোদিকে সন্দেহভাজন।
পরিবেশ আপাতদৃষ্টিতে নিরীহই। কিন্তু যত সময় যায়, সন্দেহভাজনের পক্ষে ‘নিরীহ’ থাকে না আর তেমন। লালবাজারের একটা স্থানমাহাত্ম্য আছে। গোয়েন্দাবিভাগের তো আরও। একতলার প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশের গাড়ি। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে চোখে পড়ছে পোশাকে বা প্লেন ড্রেসে পুলিশকর্মীদের ওঠানামা। চোখে পড়ছে বিভিন্ন শাখার বোর্ড। গুন্ডাদমন শাখা, ব্যাংক ফ্রড সেকশন, ডাকাতি-ছিনতাই দমন শাখা, হোমিসাইড… একটার পর একটা। হয়তো কোমরে দড়ি বেঁধে হাঁটিয়ে কোনও আসামিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে করিডর দিয়ে, কোনও নির্দিষ্ট ঘরে। যে আসামির চুপসে যাওয়া চোখমুখ দেখে মনে হবে, ঝড় নয়, শরীর-মনের উপর দিয়ে সুনামি বয়ে গেছে। মায়া হবে পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম লোকেরও।
আবহটাই এমন, কোনওরকম বলপ্রয়োগ বা ‘আদরযত্ন’ ছাড়াই অধিকাংশের স্নায়ু বিদ্রোহ করতে শুরু করে, চোখে চোখ রেখে ওই একচিলতে ঘরে যখন প্রশ্নের পর প্রশ্ন ঠান্ডা গলায় ছুটে আসতে থাকে। কপালে স্বেদবিন্দু দেখা দেয়, ফুল স্পিডে ফ্যান ঘুরতে থাকা সত্ত্বেও। থানায় বা অন্যত্র জিজ্ঞাসাবাদে কিছুতেই চিড় ধরানো যায়নি রক্ষণে, অথচ লালবাজারে এসে পোড়খাওয়া অভিযুক্তের যাবতীয় প্রতিরোধ অদৃশ্য হয়ে গেছে একঘণ্টার জেরায়, এমন যে কত দেখেছি আমরা।
সুমিত রায়কে অবশ্য বিচলিত দেখাচ্ছিল না বিশেষ। মলয়ের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে।
—হ্যাঁ, কথা বলেছি অ্যাডভোকেটের সঙ্গে। গত সাতদিনে আপনারা পাঁচবার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। বাড়িতে দু’বার, থানায় ডেকে তিনবার। আমার ধারণা হয়েছে, আপনারা আমাকে অ্যারেস্ট করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাই উকিলের কাছে গিয়েছিলাম।
—আমরা তো অন্য অনেককেও একাধিকবার ডেকে কথা বলেছি। প্রয়োজনে আবার বলব। কারও মাথায় আগাম জামিনের কথা এল না, উকিলের সঙ্গে যোগাযোগ করার প্রয়োজন শুধু আপনারই হল? এর থেকে কী বোঝা যায় বলুন তো?
—কী?
—ঠাকুরঘরে কে জিজ্ঞেস করতে না করতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন প্রমাণ করতে, আপনি কলা খাননি।
সুমিতকে একটুও প্রভাবিত দেখায় না মলয়ের খোঁচায়। চুপ করে থাকেন, এবং মলয় বলে যান একটানা।
—মোটিভ ছিল আপনার। ব্যবসা ভাল যাচ্ছিল না। ভেবেছিলেন মঞ্জুদেবীকে মেরে টাকাপয়সা পাবেন বিস্তর। কপাল মন্দ, অল্পই জুটল। বেলটা আপনিই বাজিয়েছিলেন, তারপর নেমে এসেছিলেন। ঘরে ঢুকে চা খেয়েছিলেন, তারপর বয়স্কা মহিলাকে কুপিয়ে মেরে ফেলেছিলেন। ঠিক বলছি? শুধু সঙ্গে কে ছিল সেটা জানি না এখনও। আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই। বলুন, অনেক সময় আছে।
সুমিত নির্বিকার। থেমে থেমে উত্তর দেন।
—দেখুন মি. দত্ত, আপনি যা শুনতে চাইছেন, সেটাই বলব বলে যদি ভাবেন, ভুল ভাবছেন। আপনি যা যা বললেন, সেটা আপনার থিয়োরি, আপনার কল্পনা। খুনটা আমি করিনি। আগেও বলেছি, এখনও বলছি। প্রমাণ আছে কোনও? সারাদিন ধরে এখানে বসিয়ে রাখলেও একই কথা বলব। খুনটা করিনি আমি।
পুলিশ প্রশিক্ষণের সময় জেরার যা যা পদ্ধতি শেখানো হয়, সবই প্রয়োগ করলেন মলয় কয়েক ঘণ্টা ধরে। সুমিত ভাঙলেন না, মচকালেনও না। স্রেফ সন্দেহের বশে কাউকে খুনের মামলায় গ্রেফতার করা যায় না। হয় এমন প্রমাণ লাগে যা সন্দেহভাজনের সামনে ফেললে স্বীকারোক্তি আসা অবধারিত, নয় সোজাসাপটা স্বীকারোক্তি দরকার হয় জেরার মুখে। প্রমাণ সংগ্রহ পরে, বয়ান অনুযায়ী।
কোনওটাই হাতে নেই সুমিতের বিরুদ্ধে। গ্রেফতার করে আদালতে তুললে হাসির খোরাক হতে হবে। হতাশ লাগে মলয়ের। সুমিতকে অনুমতি দেন বাড়ি যাওয়ার।
—বেশ সুমিতবাবু, আজকের মতো এটুকুই। আবার ডাকতে হতে পারে আপনাকে। আপনার কথা বিশ্বাস করলাম, এমন ভাবার কারণ নেই, এটুকু বলে রাখলাম।
সুমিত উঠতে যাবেন, মলয় বসিয়ে দেন হাত ধরে।
—চা খেয়ে যান অন্তত। না হলে লালবাজারের বদনাম হবে। এতক্ষণ কথা বললাম, আর এক কাপ চা-ও অফার করলাম না!
লালবাজারের চায়ে বা সুনাম-বদনামে এতটুকু আগ্রহী দেখায় না সুমিতকে।
—নাহ, তার দরকার নেই। আমার এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে অনেক।
—আচ্ছা, চা নয়, জল তো এক গ্লাস খেয়ে যান। না হলে ওই যে কথায় বলে না, গৃহস্থের অকল্যাণ হয়।
সুমিতকে এইবার রাগত দেখায়। পুলিশের এই ‘গৃহস্থপনা’ অসহ্য ঠেকে। একে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই ছোট্ট ঘরে বসিয়ে চাপ দিচ্ছে, মুখের উপর ‘খুনি’ বলছে। তারপর ‘জল খেয়ে যান, চা খাবেন?’-এর ন্যাকামি। নেহাত এটা লালবাজার আর এই অকালপক্ব মলয় ছোকরাটা পুলিশ অফিসার। না হলে …।
কিছু বলতে গিয়েও সুমিত সংবরণ করেন নিজেকে। জলের গ্লাস এলে ঢকঢক করে খেয়ে বেরিয়ে যান।
এবং বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ‘সায়েন্টিফিক উইং’-এর অফিসারদের ডাকেন মলয়। গ্লাসে আঙুলের ছাপ পড়েছে সুমিতের। ‘ডেভেলপ’ করে মঞ্জুদেবীর ফ্ল্যাটে আলমারি আর চায়ের কাপে পাওয়া আঙুলের ছাপের সঙ্গে ‘ম্যাচ’ করানোর জন্য টিম রওনা হয়ে যায় ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে। ডিসি ডিডি ফোন করেন ল্যাবরেটরির ডিরেক্টরকে, ‘রিপোর্টটা একটু তাড়াতাড়ি পেলে ভাল হয়।’
তাড়াতাড়িই পাওয়া গেল, এবং মলয়কে হতাশায় ডুবিয়ে সেই রিপোর্ট জানাল, ‘ম্যাচ’ করেনি ফিঙ্গারপ্রিন্ট। মিলছে না সুমিতের আঙুলের ছাপ ফ্ল্যাট থেকে পাওয়া ছাপের সঙ্গে।
এবার? অপরাধ স্বীকার করছেন না সুমিত। প্রমাণও হাতে নেই। আঙুলের ছাপও মিলল না। এবার? খুনটা তা হলে কে বা কারা করল? একদম অচেনা চোর-বদমাইশ কেউ? কিন্তু তা-ই বা হয় কী করে? সকালে কেউ করে এসব এভাবে? আর ঘুরেফিরে সেই পরিচিতির তত্ত্ব, অচেনা কাউকে দরজা খুলবেনই বা কেন মঞ্জু?
খুনটা তা হলে আনডিটেকটেড থেকে যাবে? দশ দিন হয়ে গেল। কিনারা করা গেল না, ‘এখনও অন্ধকারে পুলিশ’ জাতীয় স্টোরি তো প্রায় রোজই বেরচ্ছে খবরের কাগজে। অন্ধকারে আর কতদিন থাকতে হবে?
হতোদ্যম মলয় যখন বাড়ি ফিরছেন ১৮ নভেম্বরের রাতে, ভাবতেও পারেননি অন্ধকার কাটতে চলেছে দ্রুত। আলোর ফুলকি দেখতে পাবেন খুব শিগগিরই।
.
রুটি, আলু-গোবি, বেগুন ভর্তা।
অর্ডার দিয়ে অন্যমনস্ক বসে ছিলেন মলয়। বীরভূমে গ্রামের বাড়িতে শেষ গিয়েছেন প্রায় চার মাস হয়ে গেল। সেই জুলাইয়ে। পুজোয় ছুটিছাটার প্রশ্ন নেই। কিন্তু তারপরেও কাজের চাপে আর যাওয়া হল কই? বিজয়ার প্রণামটাও এখনও সারা হয়নি। ছুটির অ্যাপ্লিকেশন দেবেন-দেবেন করছিলেন, তার মধ্যেই এই মহিলার খুন। এখন আর কিনারা হওয়ার আগে মুখ ফুটে বলাও যাবে না ছুটির কথা। এদিকে বাড়ি থেকে রোজই ফোন আসছে মা-বাবার, ‘কবে আসবি?’
আর আসা! সপ্তাহদুয়েক হতে চলল, তদন্ত আর এগোল কই? রোজ প্রায় একডজন সোর্সের সঙ্গে কথা বলছেন। মাটি কামড়ে পড়ে আছেন। যা যা করা সম্ভব, করছেন সাধ্যমতো। অথচ না আছে ক্লু, না আছে কিছু।
খাবার এসে গেছে। চেতলার এক সোর্সের সঙ্গে দেখা করতে ভোর ভোর মলয় চলে এসেছিলেন কালীঘাট এলাকায়। তখনকার চা-টোস্ট হজম হয়ে গিয়ে এখন খিদে পেয়েছে বেজায়। রাসবিহারী মোড়ের ধাবায় ঢুকেছেন লাঞ্চ সারতে।
খাবার মুখে দিয়ে খিঁচড়ে থাকা মেজাজটা আরও খারাপ হয়ে যায় মলয়ের। একটা অদ্ভুত মশলা দেয় এরা এইসব ধাবাগুলোয়। সবজির স্বাভাবিক স্বাদটাই নষ্ট হয়ে যায়। বাড়ির রান্নার মতো হবে না ঠিকই, কিন্তু তা বলে এই?
—আর দুটো রুটি বলি?
ম্যানেজারের প্রশ্নের উত্তরে বিরক্তি লুকোতে পারেন না মলয়।
—আরে না মশাই, রান্নার যা ছিরি আপনাদের…
—কেন?
—সবজিটা খেয়ে দেখলেই বুঝবেন, কেন। কোনও স্বাদই নেই।
—কেন, সবজি তো ফ্রেশই ইউজ় করি আমরা।
ডিপার্টমেন্টে মলয় ঠান্ডা স্বভাবের ছেলে হিসেবেই পরিচিত। কিন্তু সময় খারাপ গেলে যা হয়, স্বভাববিরুদ্ধ ভাবেই হঠাৎ মেজাজ হারালেন।
—আমি গ্রামের ছেলে মশাই। এখনও বাড়ি গেলে চাষের কাজে হাত লাগাই। আমাদের ভীমগড় বাজারের সবজি খেলে বুঝতে পারতেন, কোনটা টাটকা আর কোনটা নয়। ফ্রেশ সবজি চেনাবেন না আমাকে।
ম্যানেজার আর থাকতে পারেন না।
—কিছু মনে করবেন না। রান্নার এদিক-ওদিক হতে পারে, কিন্তু বাসি মাল আমাদের এখানে পাবেন না। এখানেও টাটকা সবজিই আসে। ক্যানিং থেকে, লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে, বজবজ থেকে। ট্রেনে করে এসে লোক দিয়ে যায়। আশেপাশের ভাতের হোটেলেও দেয়। অনেক বাড়িতেও দেয়।
মলয় আর কথা বাড়ান না। খারাপই লাগে একটু। সামান্য ব্যাপারে আগ বাড়িয়ে খিটখিট না করলেই হত। বিল মিটিয়ে কাউন্টার থেকে মৌরি–মিছরি মুখে দিয়ে বেরিয়ে পড়েন। বাস্তুহারা বাজারে একজন সোর্স অপেক্ষা করছে।
কিছুটা হাঁটার পরই থমকে যান মলয়, মস্তিষ্কে হঠাৎই বিদ্যুৎঝলক। কী যেন বললেন ম্যানেজার ভদ্রলোক? ক্যানিং-লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে সবজি আসে? আর সেই সবজি আশেপাশের বাড়িতেও সাপ্লাই হয়? ক্যানিং… ক্যানিং… উষারানির বাড়ি তো ক্যানিং-এ। আর, খুনের দিন মঞ্জুদেবীর রান্নাঘরে ঝুড়িভরতি সবজি তো এখনও ভাসছে চোখের সামনে। তা হলে কি …
প্রায় ছুটেই ধাবায় ফেরেন মলয়। ম্যানেজার একটু অবাকই হন সামান্য হাঁফাতে থাকা মলয়কে দেখে।
মলয় বোঝেন, এবার আইডেন্টিটি কার্ডটা বার করা দরকার। লালবাজারের গোয়েন্দা, পরিচয় পেয়ে ম্যানেজারের ব্যবহার বদলে যায় নিমেষে। কেজো ভদ্রতার জায়গা নেয় সমীহ।
—কী ব্যাপার স্যার, কিছু ফেলে গেছেন?
—না, আচ্ছা ওই ক্যানিং-লক্ষ্মীকান্তপুর থেকে সবজি আসে বলছিলেন না? ক্যানিং থেকে কারা আসে?
—এক-দু’জন নয় স্যার, পাঁচ-ছ’জন আসে। রোজ রোজ একই লোক তো আসে না। কোনওদিন দু’জন এল, কোনওদিন হয়তো তিন বা চার। কেন স্যার? কী ব্যাপার?
—ক্যানিং থেকে সবজি শেষ কবে এসেছিল এখানে?
—পরশু, বা তরশু হবে।
—তার আগে?
—তার আগে… তার আগে… সপ্তাহখানেক আগে বোধহয়… দাঁড়ান রেজিস্টারে তো লেখা থাকে কবে কোথাকার মাল ঢুকল।
—সপ্তাহখানেক আগে যারা সবজি দিয়ে গিয়েছিল, তাদের চেহারা মনে আছে?
—না স্যার, ডেলিভারি কর্মচারীরা নেয়, আমার তো কাউন্টারে বসেই কাটে বেশিরভাগ সময়টা…
—আপনি রেজিস্টারটা বের করে রাখুন, আমি আধঘণ্টার মধ্যে আসছি ঘুরে। ডেলিভারি যারা নেয়, তাদের সঙ্গে কথা বলব।
ম্যানেজার আঁচ করতে পারেন, গুরুতর কিছু একটা ব্যাপার আছে ক্যানিং-এর সবজি নিয়ে। জিজ্ঞেস করে ফেলেন, স্যার, শুধু ক্যানিং, না লক্ষ্মীকান্তপুর-বজবজও দেখে রাখব?
—আপাতত শুধু ক্যানিং। আসছি ঘুরে।
ঘুরে আর এলেন না মলয়। প্রয়োজন পড়ল না। উষারানিকে কালীঘাট থানায় ডেকে ফের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন সাড়ে চারটে নাগাদ। প্রাথমিক জেরায় উষা বলেছিলেন, এক মেয়ে তাঁর। বিয়ে হয়ে গেছে। মেয়ে-জামাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ নেই তেমন। এবারও একই কথা বললেন। কিন্তু মলয় এবার আর সেই ভুল করলেন না, যেটা প্রথমবার করেছিলেন। মঞ্জুদেবীর মেয়ে মানসী এককথায় উষারানিকে ‘ক্লিনচিট’ দেওয়ার পর সেভাবে আর গভীরে গিয়ে নাড়াচাড়া করেননি ওঁর পরিবারের দিকটা। এবার করলেন।
—কোথায় থাকে আপনার মেয়ে-জামাই?
—ক্যানিং লাইনেই থাকে। বারুইপুরের দিকে। গ্রামের নামটা জানি না।
—মেয়ের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় না?
—না স্যার, ন’মাসে ছ’মাসে একবার।
—শেষ কবে দেখা হয়েছিল?
—মাস ছয়েক আগে স্যার। টুম্পার, মানে আমার মেয়ের বাচ্চা হওয়ার সময়। বাচ্চাটা বাঁচেনি। হাসপাতালেই মারা গিয়েছিল।
মলয় আর দুটো প্রশ্ন করেন শুধু।
—জামাইয়ের নামটা বলুন। আর বাচ্চা হওয়ার সময় কোন হাসপাতালে ভরতি হয়েছিল টুম্পা?
—সুশীল সর্দার। ক্যানিং সদর হাসপাতাল।
সন্ধেয় আর বাড়ি ফেরা হয় না উষারানির। আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বসিয়ে রাখা হয় থানায়, মহিলা পুলিশের জিম্মায়।
বাড়ি ফেরা হয় না মলয়েরও। যাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছিল, ক্যানিং-কানেকশনেই লুকিয়ে আছে রহস্যের চাবিকাঠি। ওসি হোমিসাইডকে জানালেন সব। সাত-আটজন অফিসারের টিম পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছল কালীঘাট থানায় এবং রওনা দিল পত্রপাঠ। গন্তব্য, ক্যানিং সদর হাসপাতাল।
যেতে যেতেই মোবাইলে মানসীকে ধরলেন মলয়।
—মায়ের বাজার তো আপনিই করে দিতেন, না?
—হ্যাঁ, সপ্তাহে একবার। সাত-আটদিনের বাজার করে দিয়ে আসতাম। হয় আমি, নয়তো হাজ়ব্যান্ড।
—সবজি কেনাকাটার আলাদা লোক ছিল?
—না তো! আমিই যা কেনার, কিনে দিয়ে আসতাম। কেন?
—এমনিই। অন্য কেউ তরিতরকারি দিতে আসত না, শিয়োর আপনি?
—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তেমন কেউ থাকলে আমি জানব না, হয়?
—আচ্ছা, মায়ের মৃত্যুর কতদিন আগে বাজার, আই মিন, সবজি-বাজার করে দিয়ে এসেছিলেন?
একটু ভেবে মানসী উত্তর দেন, ‘দিনপাঁচেক আগে হবে। কেন বলুন তো?’
—না, তেমন কিছু না। থ্যাঙ্ক ইউ।
কৌতূহলী মানসী আর কোনও প্রশ্ন করার আগেই ফোন রেখে দিয়েছিলেন মলয়। গাড়ি ছুটছিল ক্যানিং-এর দিকে, আর ধমনীতে অ্যাড্রিনালিনের বাড়তি ক্ষরণ দিব্যি টের পাচ্ছিলেন মলয়। সেই অনুভূতি, যা শব্দ খরচ করে বোঝানো দুঃসাধ্য। যা তদন্তকারী অফিসারমাত্রই অনুভব করেন কোনও জটিল মামলার সম্ভাব্য কিনারার অতর্কিত আভাসে। মানসী বলছেন, খুনের পাঁচ দিন আগে বাজার করে দিয়ে এসেছিলেন। আর কোন লোক ছিলও না তরিতরকারি সাপ্লাই করার। তা হলে পাঁচদিন পরও ঝুড়িভরতি সবজি থাকে কী করে? কারা দিয়ে গিয়েছিল সবজি? কবে? কখন?
ডিসি সাউথ ফোন করে রেখেছিলেন ক্যানিং হাসপাতালের সুপারকে। সুপার নিজেই উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার নিয়ে। হ্যাঁ, মাসছয়েক আগে একটি সদ্যোজাতা শিশুকন্যা মারা গিয়েছিল প্রসবের পরেই। মায়ের নাম টুম্পা সর্দার। বাবার নাম সুশীল সর্দার। ঠিকানা, বারুইপুর থানার মাঝেরহাট গ্রাম।
মলয় যখন টিম নিয়ে মাঝেরহাট গ্রামে সুশীলের বাড়িতে কড়া নাড়লেন, রাত প্রায় ন’টা। সুশীল পুলিশ দেখে হকচকিয়ে গেলেন। মলয় সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন, ‘গয়নাগাটি যা কালীঘাট থেকে পেয়েছিলেন, বার করুন, আর যেটা দিয়ে খুনটা করেছিলেন, সেটাও।’
সুশীল ‘কোন খুন? আমি কিছু জানি না!’ জাতীয় প্রতিরোধের রাস্তায় গেলেনই না। কবুল করলেন সোজাসাপটাই, ‘বলছি স্যার, সব বলছি। তবে আমি একা করিনি। কাকাও ছিল।’
—কাকা?
—স্বপন সর্দার, কাছেই থাকে।
—নিয়ে চলুন কাকার বাড়ি।
—বাড়িতে পাবেন না স্যার। বাজারে কাকার অনেক ধারদেনা। পাওনাদারদের জ্বালায় বাড়িতে থাকে না। আমি জানি কোথায় থাকে। চলুন।
স্বপনকে গ্রেফতার করা হল সুশীলের দেখিয়ে দেওয়া ডেরা থেকে। কাকা-ভাইপোকে নিয়ে গোয়েন্দাবিভাগের টিম কলকাতা রওনা দেওয়ার পর গাড়িতে গা এলিয়ে দেন মলয়। যাক, ছুটির অ্যাপ্লিকেশনটা এবার করে ফেলতে হবে। আর রাসবিহারীর ধাবার ম্যানেজার ভদ্রলোককেও একটা থ্যাঙ্কস দিয়ে আসতে হবে কাল। ভাগ্যিস সবজিটা অমন বিস্বাদ হয়েছিল, ভাগ্যিস উঠেছিল ক্যানিং-এর কথা। আছে আছে, মলয় দত্তের টেলিপ্যাথির জোর আছে!
বারুইপুর থেকে কলকাতায় ফেরার পথে মলয়কে খুনের বৃত্তান্ত খুলে বললেন সুশীল-স্বপন। জানা গেল, ঠিক কী ঘটেছিল।
সুশীলের বয়স বাইশ-তেইশ। স্বপনের মধ্যতিরিশ। দু’জনেরই রুজিরোজগার অন্যের জমিতে চাষবাস করে। মাঝেমাঝে সবজি বেচতে আসতেন কলকাতায়, হোটেল-ধাবায়।
ঘোর অর্থাভাব ছিল দু’জনেরই। সুশীলের বাবা ছিলেন প্রতিবন্ধী। মা-ও ইদানীং অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। রান্নাঘরে পড়ে গিয়ে গুরুতর চোট পেয়েছিলেন মাথায়। সংসার চালানোর পুরো দায়িত্বই ছিল সুশীলের উপর। যে দায়িত্ব দুর্বহ হয়ে উঠছিল দিনের পর দিন। চাষবাসের কাজ করে কতটুকুই বা আয় হয়? তবু কষ্টেসৃষ্টে চলে যেত কোনওরকমে। মায়ের অসুস্থতার পর অর্থসংকট গভীর হয়েছিল। চিকিৎসার খরচেই মাসিক উপার্জনের অর্ধেক টাকা বেরিয়ে যাচ্ছিল। বছর দুয়েক আগে বিয়ে করার পর এমনিই খরচ বেড়েছিল সংসারের। টুম্পার ছোটখাটো সাধ-আহ্লাদ মেটাতে পারতেন আগে। এখন সে পাটও চুকেছে। বউয়ের মুখ আজকাল গোমড়াই থাকে সারাক্ষণ।
এভাবে আর কতদিন? রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবতেন সুশীল। ঘটিবাটি বন্ধক রাখতে হবে এবার। কিন্তু তা দিয়েই বা কী হবে? বাড়িতে কী-ই বা আছে তেমন দামি কিছু? খেয়েপরে বাঁচতে গেলে, মায়ের চিকিৎসা চালাতে গেলে, টাকার দরকার। বেশ কিছু টাকার। কে দেবে? ধার নিলে আর এক বিপদ। শোধ তো দিতে হবে সুদসহ। না পারলে কাকার মতো অবস্থা হবে।
‘কাকার মতো অবস্থা’ মানে পাওনাদারদের তাগাদায় ভিটেছাড়া হওয়া। স্বপন সর্দারের জুয়ার নেশা ছিল দুরারোগ্য পর্যায়ের। যা রোজগার করতেন, পুরোটাই উড়িয়ে দিতেন জুয়ার ঠেকে। ফলে অবধারিত আর্থিক অনটন এবং পেট চালাতে ধার করা। পাওনাদাররা সকাল-সন্ধে হানা দিত স্বপনের বাড়িতে। ধার শোধ দিতে অপারগ স্বপন বাধ্য হয়েছিলেন বাড়ির মায়া ত্যাগ করতে। আজ এখানে, কাল ওখানে, পরশু সেখানে, এ-ভাবেই কাটত।
কাকার মতো পালিয়ে পালিয়ে বেড়ানো অসম্ভব মা-বাবা-বউকে ছেড়ে। তার চেয়ে
চুরি-ডাকাতি করাই বোধহয় ভাল। যা হবে, দেখা যাবে। আকাশপাতাল ভাবতে ভাবতেই একদিন মাথায় এল কালীঘাটের ‘দিদার’ কথা। টুম্পার মা ওই বাড়িতে অনেক বছর ধরে কাজ করেন। বিয়ের পর টুম্পাকে নিয়ে গিয়েছিলেন একবার ওই ফ্ল্যাটে। শাশুড়িই নিয়ে গিয়েছিলেন মেয়ে-জামাইকে। ওই দিদার কাছে টাকা ধার চাইলে কেমন হয়? কিন্তু যদি না দেয়? কথা নেই বার্তা নেই, এতদিন পরে হুট করে গিয়ে টাকা চাইলে না দেওয়ারই কথা। না দিলে? সুশীল মনস্থির করে ফেলেন।
পরের সন্ধেয় কাকা-ভাইপোর দেখা হয়। সুশীল খুলে বলেন প্ল্যান।
—কালীঘাটে এক বুড়ি দিদার বাড়ি চিনি আমি। দাদু মারা গেছে। দাদু-দিদা দু’জনেই ভাল চাকরি করত। গিয়ে টাকা চাইব। না দিলে কেড়ে নেব। যাবে?
না গিয়ে উপায়ও ছিল না স্বপনের। আর্থিক সংকট থেকে রেহাই পেতে তিনিও একই রকম মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। স্বপন রাজি হয়ে গেলেন। এবং ৬ নভেম্বর ভোরের ট্রেনে চড়ে বসলেন কাকা-ভাইপো। খুন-জখম বাদ দিন, ছিঁচকে চুরি বা পকেটমারিরও কোনও পূর্বইতিহাস ছিল না যাঁদের।
সুশীল একটা ছুরি নিলেন সঙ্গে। আর একটা চটের ব্যাগ মাঝারি সাইজ়ের। যাতে রইল টাটকা সবজি কিছু।
মঞ্জুর ফ্ল্যাটে বেল বাজল ন’টা নাগাদ। উষা এবং জগদীশ তখন কাজ সেরে বেরিয়ে গেছেন। মঞ্জু বাড়িতে একা। ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কে?’
—দিদা, আমি সুশীল। উষার জামাই। আপনার জন্য একটু টাটকা সবজি নিয়ে এসেছি। এদিকে কাজে এসেছিলাম, ভাবলাম দেখা করে যাই।
অচেনা লোক নয়, উষার জামাই। আগেও এসেছে একবার। মঞ্জু দরজা খুলে দিলেন। সুশীল ফ্ল্যাটে ঢুকলেন কাকাকে নিয়ে।
—দিদা, এঁর নাম স্বপন। আমার কাকা।
চটের ব্যাগ থেকে সবজি বার করলেন সুশীল। মঞ্জু রেখে এলেন রান্নাঘরের ঝুড়িতে। এতদূর থেকে সবজি নিয়ে এসেছে, এক কাপ চা না খাওয়ালে খারাপ দেখায়। উষাকে নিজের মেয়ের মতোই ভালবাসেন। তার জামাইকে চট করে বিদায় করে দেওয়া যায় না। সুশীল-স্বপনকে নিজের ঘরে বসিয়ে চা তৈরি করতে রান্নাঘরে ঢুকলেন মঞ্জু। নিজের জন্যও বানালেন এক কাপ।
চা খেতে খেতে এটা-সেটা কথার মধ্যেই সুশীল পাড়লেন টাকার কথা। বড্ড টানাটানি যাচ্ছে, কিছু টাকা ধার পেলে ভাল হয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শোধ দিয়ে দেবেন। মঞ্জু এবার বিরক্ত হলেন। এ যে দেখি খেতে পেলে শুতে চায়! সটান বলে দিলেন, ‘টাকা দিতে পারব না। আর উষা জানে, তোমরা এসেছ আজ?’ সুশীল যেটা সত্যি, সেটাই বললেন। উষা সত্যিই জানতেন না জামাই এবং তার কাকার এই প্ল্যানের বিন্দুবিসর্গও।
‘তোমরা এখন যাও’ বলে ডাইনিং টেবিলের চেয়ার ছেড়ে মঞ্জু উঠে দাঁড়ানো মাত্রই তাঁর হাত চেপে ধরলেন সুশীল। বাকিটা রইল সুশীলেরই বয়ানে।
—দিদার হাত থেকে চায়ের কাপ পড়ে গেল। দিদা চিৎকার করতে যেতেই কাকা ডাইনিং টেবিলের কোণে পড়ে থাকা একটা কাপড় দিয়ে মুখ চেপে ধরল। তারপর মুখে ঘুসি মারল খুব জোরে। আমি ছুরিটা বার করলাম। আমাদের তো চিনেই গেছে। মেরে ফেলা ছাড়া উপায়ও নেই। না হলে জেলের ঘানি টানতে হবে। গলায় চালালাম ছুরি। তারপর পেটে।
দিদা যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে নিস্তেজ হয়ে পড়ল। আমি ছুরিটা দিদার নাইটিতে মুছে নিলাম। রেখে দিলাম ব্যাগে। অনেক চেষ্টা করেও আলমারিটা খুলতে পারলাম না। চাবিই পেলাম না। ক্যাশ বলতে পেলাম বাইরে এদিক-ওদিক যা ছিল ব্যাগে-ট্যাগে, হাজার দুয়েক মতো। দিদার গলা থেকে সোনার চেন আর হাত থেকে চুড়ি খুলে নিলাম। যখন এসব চলছিল, তখন একবার বেল বেজেছিল। আমরা খুলিনি। একটু পরে চুপচাপ দরজা খুলে ফাঁক করে যখন দেখেছি কেউ নেই, তখন চট করে নেমে গিয়েছি।
মলয় বোঝেন, ওই যে একবার বেল বেজেছিল, ওটা শুভঙ্কর বাজিয়েছিলেন। আনন্দবাজারের কর্মী।
সাক্ষ্যপ্রমাণ ছিল ঠাসবুনোট। যে ব্যাগে ছুরি নিয়ে এসেছিলেন, ফেরার ট্রেন ধরার সময় বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে একটা ঝোপের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলেন সুশীল। বয়ান অনুযায়ী উদ্ধার হল সেই ছুরি। লুঠ করা গয়না বারুইপুরের এক দোকানে বন্ধক রেখেছিলেন স্বপন। উদ্ধার হল সেগুলোও, দোকানি আদালতে চিহ্নিত করলেন স্বপনকে। আর মানসী শনাক্ত করলেন মায়ের গয়না।
আলমারি আর চায়ের কাপে পাওয়া আঙুলের ছাপের সঙ্গে মিলে গেল আততায়ীদের ফিঙ্গারপ্রিন্ট। স্বপন একটা আংটি পরতেন ডান হাতে। যে হাতে মঞ্জুকে ঘুসিটা মেরেছিলেন, গাল ছড়ে গেছিল মঞ্জুর। ওই ‘abrasive wound’ যে আংটির আঘাতে হওয়া সম্ভব, তারও উল্লেখ ছিল ফরেনসিক রিপোর্টে। সর্বোপরি আদালতে স্বপন স্বেচ্ছায় জবানবন্দিও দিয়েছিলেন, ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে।
২০১৭-র সেপ্টেম্বরে রায় বেরিয়েছিল। দোষী সাব্যস্ত করে সুশীল-স্বপনকে যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডিত করেছিলেন বিচারক।
পরিচিত ভেবে মঞ্জু দরজা খুলেছিলেন, বিশ্বাস করে। চা খাইয়েছিলেন। তারপর খুন হয়ে গিয়েছিলেন। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো যেমন পাপ, কখনও কখনও মানুষকে বিশ্বাস করাও? শেষ বিচারে তা হলে কী দাঁড়ায় এ মামলার নির্যাস?
বিশ্বাসই বিশ্বাসঘাতক।
২.১০ ত্রিনয়ন ও ত্রিনয়ন
[কার্ড ক্লোনিং মামলা
সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়, বড়বাজার থানার ওসি। ২০১০ সালে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রদত্ত ‘প্রশংসা পদক’-এ সম্মানিত। ২০১৪ সালে পেয়েছেন ভারত সরকারের ‘ইন্ডিয়ান পুলিশ মেডেল’।]
একবার দেখলে আরেকবার তাকাতে ইচ্ছে হয়।
মহিলা সত্যিই চোখ টানার মতো সুন্দরী। দেখে মনে হয় বয়স মাঝতিরিশ। ববকাট চুলে আঙুল চালাচ্ছেন ট্যাক্সি থেকে নেমে। যেটা এসে থেমেছে বিমানবন্দরের অ্যারাইভাল গেটের ঠিক সামনে।
প্রি-পেইড ট্যাক্সি বুথের বাইরে দাঁড়িয়ে চারপাশে চোখ বুলোচ্ছিলেন সৌম্য। দেখার মতো কিছু থাকে না এয়ারপোর্টে। কী বাইরে, কী ভিতরে। সব শহরেই একই ছবি। একই ধাঁচের বিল্ডিং। একের পর এক গাড়ি এসে থামছে বাইরের রাস্তায়। হয় অ্যারাইভালে, নয় ডিপার্চারে।
যাঁরা উড়ে যাবেন অন্য শহরে, তাঁরা লাগেজ ট্রলি টেনে এনে মালপত্তর রাখছেন। এগোচ্ছেন এন্ট্রি গেটের দিকে। যাঁরা ঝাড়া হাত-পা, তাঁরা গাড়ি থেকে নেমে আরও আগে পৌঁছে যাচ্ছেন গেটে। যন্ত্রও লজ্জা পাবে, এমন মুখ করে টিকিট চেক করছেন বিমানবন্দরের কর্মী। সজাগ দৃষ্টি নিয়ে লক্ষ করছেন পাশে দাঁড়ানো সশস্ত্র নিরাপত্তারক্ষী।
যাঁদের উড়ান এই শহরমুখী, বেরনোর গেটে তাঁদের জন্য ভিড়। আত্মীয়স্বজন যত, তার থেকে বেশি জটলা ড্রাইভারদের। একটু পরেই যাঁরা আরোহী হবেন পার্কিংয়ে থাকা গাড়িগুলোর, তাঁদের নাম লেখা প্ল্যাকার্ড নিয়ে অপেক্ষমাণ। চোখ ডিসপ্লে বোর্ডের দিকে। যার লেখাগুলো ঘনঘন পালটাচ্ছে। অমুক ফ্লাইট ইজ় ডিলেইড। তমুক ফ্লাইট হ্যাজ় জাস্ট ল্যান্ডেড।
এয়ারপোর্ট বড্ড একঘেয়ে লাগে সৌম্যর। শহরের নামটা শুধু বদলে দিলেই হল। বাকি সব মোটামুটি উনিশ-বিশ। বাইরের ভিড়ের মধ্যেও একটা দমবন্ধ শৃঙ্খলা। চলো নিয়মমতে। এর থেকে স্টেশন ভাল। তুমুল ভিড়ভাট্টা আছে। পারিপাট্যের অভাব আছে। হকারের হইহই আছে। কিন্তু চরিত্র আছে। প্রাণ আছে। এক এক শহরে এক এক রকমের স্থাপত্য। শুধু নাম বদলায় না। বাড়িও বদলে যায়।
এলোমেলো ভাবনায় ছেদ পড়ে সঙ্গী অফিসারের কনুইয়ের গুঁতোয়।
—স্যার… ওই দেখুন.. লিন্ডা!
সতীর্থের দৃষ্টিপথ অনুসরণ করেন সৌম্য। ববকাট চুলের সুন্দরী দাঁড়িয়ে পড়েছেন বেরিয়ে আসার গেটের সামনে। একবার চোখ রাখলেন কবজিতে বাঁধা ঘড়িতে। তাকালেন ডিসপ্লে বোর্ডে।
কোন ফ্লাইটের জন্য অপেক্ষা করছেন মহিলা, জানা ছিল সৌম্য এবং সঙ্গীদের। দুবাই টু কলকাতা, এমিরেটস-এর উড়ান কলকাতার মাটি ছুঁল আধঘণ্টার মধ্যেই। অন্য অনেকের সঙ্গে বেরিয়ে এলেন এক সুগঠিত চেহারার যুবক। যাঁকে বেরতে দেখেই এগিয়ে গেলেন মহিলা। জড়িয়ে ধরলেন আলতো। এবং আলিঙ্গনপর্ব শেষ হতে না হতেই দেখলেন, দুই মহিলা সহ চারজন ঘিরে ধরেছেন আচমকা। যাঁদের একজন সরাসরি যুবকের হাত চেপে ধরেছেন, কোনও ভূমিকা না করেই অল্প কথায় বলেছেন, যা বলার ছিল।
—ইয়োর গেম ইজ় আপ..
—হোয়াট? হোয়াট গেম আর ইউ টকিং অ্যাবাউট? আই ডোন্ট গেট দিস …
কৌতূহলী ভিড় জমার আগেই পকেট থেকে আই কার্ড বার করেন সৌম্য, মেলে ধরেন দুবাই থেকে সদ্য কলকাতায় আসা যুবকের সামনে। সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট, কলকাতা পুলিশ।
জোঁকের মুখে নুন পড়লে যা অবধারিত, চোখমুখ নিমেষে রক্তশূন্য হয়ে যায় যুবকের। মহিলারও। মিনিটখানেকের মধ্যেই একটা টাটা সুমো এসে থামে গেটের সামনে। যাতে দু’জনকে চাপিয়ে গাড়ি বেরয় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে।
গন্তব্য? কোথায় আর? গোয়েন্দাপীঠ লালবাজার!
.
গোওওওল! বল জড়িয়ে গেছে জালে। তারপর যা হয়, গোলদাতাকে ঘিরে উচ্ছ্বাস এক দলের। গোলকিপারকে নিয়ে হা-হুতাশ বিপক্ষের।
শীতশেষের ফেব্রুয়ারিতে ফুটবলের তেমন চল নেই কলকাতা ময়দানে। ব্যাটে-বলেরই দাপট থাকে ওসময়টা। ময়দানের এই মাঠটায় ছেলেগুলো তবু দিব্যি ফুটবল পেটাচ্ছে। অফ সিজ়ন প্র্যাকটিস?
মাঠের বাইরে একটা চেয়ারে বসে লাল-কালো ট্র্যাকসুট পরিহিত যিনি নজর রাখছেন ছেলেগুলোর উপর, তাঁর দিকে এগিয়ে যান দুই যুবক। নিয়মরক্ষার আলাপ-পরিচয়ের পর সোজাসুজি আর্জি জানান।
—দাদা, আমাদের একটা ভাল স্ট্রাইকার চাই। বলটা যে মোক্ষম সময়ে তিন কাঠির মধ্যে রাখতে পারবে। গোল করার লোক নেই আমাদের টিমে।
লাল-কালো ট্র্যাকসুট চুপ করে শুনলেন। এবং তারও মিনিটখানেক পর সামান্য হাসলেন। সে হাসি দেখে ‘গুপী গাইন বাঘা বাইন’ মনে পড়ে যায় দুই যুবকের। শুণ্ডির রাজা মেয়ের জন্য পাত্র হিসেবে গুপীকে ভেবে রেখেছেন শুনে বাঘার মাথায় বজ্রাঘাত। উদভ্রান্ত বাঘাকে আশ্বস্ত করে হল্লারাজার টিপ্পনী, ‘রাজকন্যা কি কম পড়িতেছে?’ অবিকল সেই হাসি ভদ্রলোকের মুখে। শুধু ‘রাজকন্যা’-র বদলে ‘ফুটবলার’ বসিয়ে দিতে হবে, এই যা। শেষ দৃশ্য ‘আর কম পড়িতেছে?’—মার্কা হাসি।
—স্ট্রাইকার? পাচ্ছেন না? তা বাজেট কত আপনাদের?
—আপনিই বলুন মিল্টনদা, কত দিতে হবে? আসলে সঞ্জয়ের হঠাৎ চোট হয়ে গেল। সঞ্জয়, আমাদের টপ গোলস্কোরার। লিগামেন্ট টিয়ার, মাঠে ফিরতে ফিরতে বেশ কয়েক মাস তো বটেই। এদিকে পাঁচ দিন পরে ফাইনাল… ভাল স্ট্রাইকার ছাড়া কোনও চান্স নেই আমাদের।
—খেলা কোথায়? কত মিনিটের?
—পাইকপাড়ায়। এই খেপ টুর্নামেন্টটা প্রতি বছর এ সময়েই হয়। সত্তর মিনিট। থার্টিফাইভ – থার্টিফাইভ।
—হুঁ, বিদেশি ছেলে আছে একটা। বেনসন। গত বছর কলকাতা লিগের সেকেন্ড ডিভিশনে খেলেছে। তেরোটা গোল করেছে। দু’পায়েই ভাল শট আছে। হেডটাও ভাল। সিক্স ফিট প্লাস… হাইটটা কাজে লাগাতে জানে।
হাতে যেন চাঁদ পান দুই যুবক।
—ওর কথা আমরাও শুনেছি। ওকে পেলে তো কথাই নেই কোনও… ইন ফ্যাক্ট, ওর জন্যই আসা… দিন আমাদের ছেলেটাকে… প্লিজ় দাদা… আমরা জানি, আপনি যেখানে খেলতে বলেন, সেখানেই খেলে ও।
তৃপ্তির হাসি হাসেন ‘দাদা’। মধ্যপঞ্চাশের মিল্টনদা। ‘প্রাচীন ময়দান প্রবাদ’ অনুযায়ী যিনি এখানে-ওখানে ছোটখাটো ‘খেপ’ টুর্নামেন্টে ফুটবলার সাপ্লাইয়ে ডক্টরেট করে ফেলেছেন।
—ম্যাচ প্রতি পাঁচ হাজার নেয়। পোষাবে?
সোজাসাপটা কথা। তেল মাখতে গেলে কড়ি ফেলতে হবে। মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন দুই যুগল।
—পাঁচ? একটা ম্যাচের জন্য একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে… কিন্তু আপনি যখন বলছেন গোলটা ভাল চেনে, তখন না হয় পাঁচই দেব। ফাইনালটা জিততেই হবে যে ভাবে হোক। প্রেস্টিজ়ের ব্যাপার..
ফের একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসেন মিল্টনদা।
—আমি যখন বলছি মানে? না ভাই .. আমি বলছি বলে দিতে হবে না। নিজেরাই দেখে নিতে পারেন। পরশু বেনসন একটা খেপ খেলতে যাবে। ইচ্ছে করলে গিয়ে দেখে নেবেন। টাকাপয়সার কথা না হয় তারপর হবে।
—না… মানে… আমরা ঠিক ওভাবে বলতে চাইনি… আসলে অনেকগুলো টাকা তো… কোথায় খেলা পরশু?
—হাওড়ায়। সাঁতরাগাছি পেরিয়ে। বিকেল তিনটেয়।
হাওড়ার মাঠটা ঠিক কোথায়, মিল্টনের কাছ থেকে বুঝে নিয়ে হাঁটা দেন ওঁরা দু’জন। যাঁদের একজন প্রশ্ন করেন অন্যকে, ‘সেভেন্টি মিনিটের ম্যাচে পাঁচ হাজারটা একটু বাড়াবাড়ি না!’
উত্তরও আসে চাঁচাছোলা, ‘ওটা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। দশ চাইলেও দিতে হত, বিশ চাইলেও দিতে হত, জানিসই তো!’
.
—আমরা জাস্ট ক্লুলেস স্যার… এমন তো কখনও হয়নি আগে!
শুনতে শুনতে কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে নগরপালের। এটা তো নতুন ধরনের ক্রাইম। এ শহরে অন্তত এর আগে হয়নি। বাকি দেশেও হয়েছে কি? মনে তো হয় না।
আইসিআইসিআই ব্যাংকের RCU (Risk Containment Unit, গ্রাহক এবং ব্যাংক, আদানপ্রদানের প্রক্রিয়া যাতে দুই তরফেই থাকে যথাসম্ভব ঝুঁকিহীন, সেই শাখা)-এর প্রধান রীতিমতো ঘামছিলেন ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে।
—আমরা বুঝতে পারছি না কী করব … ফিনান্সিয়াল লস কুড়ি লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে। হেড অফিস থেকে রোজ ফোন, রোজ মেল। পাগল হয়ে যাওয়ার জোগাড়। আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম, টেকনিক্যাল কোনও প্রবলেম, যেটা ইন্টারন্যালি সর্ট আউট হয়ে যাবে। কিন্তু হচ্ছে না… প্লিজ় ডু সামথিং স্যার।
—কী ব্যাপার? কীসের লস?
—সংক্ষেপে, বিভিন্ন ব্যাংকের গ্রাহকদের এটিএম কার্ডের তথ্য কোনওভাবে জেনে যাচ্ছে জালিয়াতরা। ধরুন, আমেরিকার ব্যাংকে মার্কিন নাগরিক রামের টাকা রাখা আছে। রামের কাছে সেই ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ড আছে। সেই কার্ডের যাবতীয় তথ্য চুরি হয়ে ঢুকে যাচ্ছে এদেশের কোনও ব্যাংকের গ্রাহক শ্যামের ক্রেডিট কার্ডে। রামের কার্ডের ব্যালান্স নিয়ে শ্যাম দেদার কেনাকাটা করে চলেছে। এইভাবেই যদুর টাকা নিয়ে মধু।
এবার রাম যখন জানতে পারছে যে তার টাকা অন্য কেউ হাওয়া করে দিয়েছে, স্বাভাবিকভাবেই দ্বারস্থ হচ্ছে ব্যাংকের। ফেটে পড়ছে ক্ষোভে। ব্যাংকের কাছে দাবি করছে লোপাট হয়ে যাওয়া টাকার ক্ষতিপূরণ। মার্কিন ব্যাংক তখন আর কী করবে? ভারতের যে ব্যাংকের ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে জালিয়াতিটা হয়েছে, তাদের কাছে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ সহ চিঠি পাঠাচ্ছে, ‘আমাদের গ্রাহকের হকের টাকা ফেরত দাও।’ ফেরত না দিয়ে উপায় নেই। দিতে হচ্ছে, এবং ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে চলেছে।
আইসিআইসিআই ব্যাংক শিকার হয়েছে এই জালিয়াতির। যার ব্যাপ্তি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে ক্রমশ। দশ-বিশ হাজারের ব্যাপার নয়। ক্ষতির অঙ্ক লাখ ছাড়িয়ে কোটি ছুঁয়ে ফেলবে এভাবে চললে।
নগরপাল প্রশ্ন করেন ব্যাংককর্তাকে, ‘আপনাদের ইন্টারন্যাল এনকোয়ারি কী বলছে?’
—সেটা তো চলছেই স্যার। কিন্তু ট্র্যাক পাওয়া যাচ্ছে না কিছু। গত পরশু অবশ্য একটা জিনিস ঘটেছে।
—কী?
—শহরের যেখানে যেখানে আমাদের EDC (Electronic Data Counter) আছে, সবাইকে আমরা অ্যালার্ট করে দিয়েছিলাম। বউবাজারের একটা দোকানে একটা ছেলে গতকাল বেশ দামি একটা সোনার চেন কিনে ক্রেডিট কার্ড দিয়েছিল। কার্ড দেখে দোকানের লোকের একটু সন্দেহ হয়। ছেলেটার কাছে আইডি প্রুফ দেখতে চাওয়া হয়। তখন এটা দিয়েছিল। এই যে…
পকেটে হাত ঢুকিয়ে যে কাগজটা বার করে আনেন ভদ্রলোক, সেটা একটা ড্রাইভিং লাইসেন্সের জেরক্স। মুখের অবয়ব আবছা।
—স্যার, আমরা ভেরিফাই করেছি মোটর ভেহিকলস থেকে। এটা জাল।
নগরপাল চোখ বুলোন জেরক্সটায়। লাইসেন্সে নাম, মহম্মদ সিকন্দর।
—ঠিক আছে। একটা লিখিত অভিযোগ করুন লোকাল থানায়। রেজিস্টার্ড হয়ে যাক কেসটা।
ভদ্রলোক বেরিয়ে যাওয়ার পর ইন্টারকমে ডিসি ডিডি-কে ধরেন সিপি।
—Anti Bank Fraud সেকশনের অফিসারদের নিয়ে বসতে চাই একবার। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।
.
কার্ড স্কিমিং(Card Skimming)। শব্দ দুটো এখন শুধু পুলিশ নয়, প্রায় সবাই জেনে গেছেন। খবরের কাগজের দৌলতে স্কিমিং নিয়ে একটা প্রাথমিক ধারণাও হয়ে গেছে অনেকেরই। কয়েকমাস আগে এটিএম জালিয়াতি নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছিল কলকাতায়। বহু মানুষের টাকা লোপাট হয়ে গিয়েছিল। মূল চক্রী ছিল কয়েকজন রোমানিয়ান নাগরিক। খুব দ্রুত যাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধরা গিয়েছিল বলে রক্ষে। না হলে আরও কত মানুষের কষ্টের টাকা যে বেমালুম উধাও হয়ে যেত, ঠিকঠিকানা নেই।
এ কাহিনি আজ থেকে আট বছর আগের। তখন ‘কার্ড স্কিমিং’ ব্যাপারটা যে কী, খায় না মাথায় দেয়, খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল না অফিসারদের। শব্দ দুটো শোনা ছিল বড়জোর, এই পর্যন্তই। ‘Anti Bank Fraud’ বিভাগটাই চালু হয়েছিল মাত্র বারো বছর আগে। ২০০৬ সালে।
ব্যাংকের তরফে শেক্সপিয়র সরণি থানায় যে মামলাটা দায়ের করা হল, তার তদন্তভার পড়ল সাব-ইনস্পেকটর সৌম্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের (বর্তমানে বড়বাজার থানার ওসি) উপর। সিপি অফিসারদের সঙ্গে বৈঠকে বুঝিয়ে বললেন স্কিমিংয়ের ব্যাপারে। এবং স্পষ্ট জানালেন, দ্রুত কিনারা করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হবে। এই জালিয়াতি চলতে থাকলে একটা সময় ব্যাংকিং ব্যবস্থার কাঠামোটাই নড়বড়ে হয়ে যাবে। সাধারণ মানুষের টাকা আর নিরাপদ থাকবে না। সুতরাং চাই অঙ্কুরেই বিনাশ।
অঙ্কুরে বিনাশ বললেই তো আর হল না। অপরাধের কী-কেন-কখন জানলে তবেই না অপরাধীর খোঁজ! ইন্টারনেট ঘেঁটে, বইপত্র পড়ে স্কিমিং সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণা তৈরি করলেন সৌম্য। যথাসাধ্য বোঝালেন সতীর্থদেরও।
ক্রেডিট কার্ডের পিছনে যে বাদামি রঙের রেখাটা থাকে, তার মধ্যে অদৃশ্যভাবে ঢোকানো থাকে কিছু তথ্য। যা সাধারণ ব্যাংক কর্মচারীদেরও জানার কথা নয়। সেই তথ্য চুরি করল কেউ। এবং প্রযুক্তির সাহায্যে অন্য ক্রেডিট কার্ডের পিছনের বাদামি রেখাটার ভিতর ঢুকিয়ে সেই কার্ড ব্যবহার করল। এটাই ‘স্কিমিং’। কিন্তু চুরিটা হয় কী করে?
আপনি এটিএম কাউন্টারে গেলেন। কম্পিউটার স্ক্রিনের নীচে যেখানে একটা সবুজ রঙের যন্ত্রে লেখা থাকে, ‘Insert your card here’, সেখানে নিয়মমতো কার্ড ঢোকালেন। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও টের পেলেন না যে ওই যন্ত্রটির ওপরে লাগানো একটা অন্য যন্ত্রে (স্কিমিং ডিভাইস) মুহূর্তে রেকর্ড হয়ে গেল কার্ডে সঞ্চিত তথ্য। এরপর কি-বোর্ডে টাইপ করলেন গোপন পিন নাম্বার। কিন্তু বুঝতে পারলেন না কি-বোর্ডের উপর নিখুঁত লাগানো আরেকটা কি-বোর্ডের মতোই দেখতে যন্ত্রের মাধ্যমে রেকর্ড হয়ে গেল আপনার পিন নাম্বার।
এটিএম ছেড়ে আপনি বেরিয়ে গেলে বাকিটা ‘এসো ভাই, বোসো ভাই, ভাত বেড়ে দি, খাবে ভাই?’-এর মতো সোজা। জালিয়াতরা কাউন্টারে ঢুকে খুলে নিয়ে গেল সেই স্কিমিং ডিভাইস, যেটা তারা আগে থেকে লাগিয়ে রেখে গিয়েছিল। এবার চুরি করা তথ্যের মাধ্যমে ডামি কার্ড তৈরি করা এবং অন্যের টাকা আত্মসাৎ করা কোনও ব্যাপারই না।
আইসিআইসিআই ব্যাংকের ক্ষেত্রে ঠিক কী ঘটেছিল, নগরপালকে যা সংক্ষেপে বলেছিলেন ব্যাংককর্তা, সেটা আরও বিশদে জানলেন সৌম্য। কী? ধরা যাক, আজকের বাজারে ভারতীয় মুদ্রায় ১ ডলারের বিনিময়মূল্য ৭০ টাকা। এবার ধরুন, কোনও মার্কিন ভদ্রলোকের ক্রেডিট কার্ডের তথ্য চুরি করল কেউ। তথ্য চলে এল ভারতে, শাগরেদের কাছে। ভুল ঠিকানা দিয়ে একটা ভারতীয় ক্রেডিট কার্ড যে আগেই তুলে রেখেছিল। যাতে ব্যালান্স ছিল জিরো।
এবার শাগরেদ কী করল, সোনার দোকানে গিয়ে ১০০ ডলার খরচ করে গয়নাগাটি কিনল। মানে, সাত হাজার টাকার গয়না। মার্কিন ভদ্রলোকের কার্ড থেকে ১০০ ডলার লোপাট হয়ে গেল। এবং চোর গয়না নিয়ে চম্পট। দোকানের মালিক জানলেন না, অমুকের কার্ডের তথ্য নিয়ে তমুককে গয়না বেচে দিলেন। বেচার সময় কার্ডটা দোকানে রাখা ছোট্ট মেশিনটায় ঘষে একটা ‘চার্জস্লিপ’ নামের যে চিরকুট বেরল, সেই স্লিপ ব্যাংকে জমা দিয়ে পরের দিন সাত হাজার টাকা তুলেও নিলেন দোকানি।
টনক নড়ল কখন? যখন সেই মার্কিন ভদ্রলোক নিজের ব্যাংকে গিয়ে হইচই করলেন। এটা কী ব্যাপার? আমার কার্ড থেকে সাত হাজার টাকার গয়না কেনাকাটার খরচ দেখানো হয়েছে। তা-ও আবার ভারতে গিয়ে। ইয়ার্কি নাকি? ভারতে যাইই নি কখনও! সত্যিই যাননি, পাসপোর্ট জানান দিচ্ছে স্পষ্ট। আমেরিকার ব্যাংক এবার ভারতীয় ব্যাংকের কাছে ১০০ ডলার চেয়ে পাঠাল অকাট্য তথ্যপ্রমাণ সমেত। ভারতীয় ব্যাংক নিজের কোষাগার থেকে টাকা দিতে বাধ্য হল। অথচ গয়নার দোকানদারকে সেই টাকাটা আগেই দিয়ে দেওয়া হয়েছে চার্জস্লিপ অনুযায়ী। গয়না কেনার নথি তো কার্ডে ঠিকঠাকই ছিল। দোকানে খোঁজ নেওয়া হল। দোকানি বললেন, কোনও বিদেশি ওই গয়না কেনেনি। তা হলে?
‘তা হলে’-র একটাই উত্তর। বিদেশি ভদ্রলোকের কার্ডের তথ্য চুরি করে ভারতীয় কার্ডে সেই তথ্য ঢুকিয়ে রাখা হয়েছিল। স্কিমিং! যার জেরে আইসিআইসিআই ব্যাংককে লক্ষ লক্ষ টাকা খেসারত দিতে হচ্ছিল।
দেশের কোথাও তখনও, সেই ২০১০ সালে, এমন কোনও ঘটনা লিপিবদ্ধ নয়, যেখানে ‘কার্ড স্কিমিং’ করে লক্ষ লক্ষ টাকা নয়ছয় হয়েছে। সাম্প্রতিক এটিএম জালিয়াতিতে রোমানিয়ার নাগরিকরা জড়িত ছিল। ভারতীয়দের কার্ডের তথ্য চুরি করে দুষ্কর্মটা ভারতীয় ব্যাংকের এটিএম-এই হয়েছিল। কিন্তু দশ বছর আগের এই মামলায় অবশ্য দেখা যাচ্ছিল, বেশ কিছু ক্ষেত্রে বিদেশে বসবাসকারী নাগরিকের কার্ডের তথ্য চুরি করে ‘স্কিমিং’ করা হয়েছে ভারতে। মানে, চক্র বিস্তৃত আমেরিকা পর্যন্ত!
ঘোর দুশ্চিন্তার কারণ ছিল লালবাজারের। এক তো এ ধরনের অপরাধ ঘটেছে প্রথম। তদন্তের পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। দুই, চক্রের একাংশ যদি থাকে বিদেশে, আর বাকিটা এদেশে, একটা আন্তর্জাতিক মাত্রা পেয়ে যায় পুরো ব্যাপারটা। কিন্তু তা বলে তো আর হাত গুটিয়ে বসে থাকা চলে না। এই গ্যাংটাকে ধরতে তো হবে।
‘ধরতে হবে’ ভাবা এক, আর ‘ধরা’ আরেক। ‘লাও তো বটে, কিন্তু আনে কে!’ চেনা ছকের বাইরে অপরাধ। কাজে আসবে না সোর্স নেটওয়ার্ক। পুলিশই ভাল করে জানত না, কীভাবে এই জালিয়াতিটা করা যায়। সোর্স কী করে জানবে? অপরাধীদের সম্পর্কে কিছু ‘ক্লু’ পেলে তবেই সোর্সকে কাজে লাগানোর প্রশ্ন। আপাতত হাতে তথ্য কী? শুধু ওই জাল ড্রাইভিং লাইসেন্সের জেরক্স। আবছা মুখাবয়ব। নাম মহম্মদ সিকন্দর।
শহরের থানাগুলোকে সতর্ক করা হল। খবর পৌঁছে দেওয়া হল এলাকার সেই সমস্ত দোকানগুলোতে, যেখানে কার্ডের মাধ্যমে কেনাকাটার ব্যবস্থা রয়েছে। বলে দেওয়া হল, কেনাবেচার সময় চোখ-কান খোলা রাখতে। কোনও কার্ডের ব্যাপারে ন্যূনতম সন্দেহ হলেই পুলিশকে জানাতে সঙ্গে সঙ্গে। এবং মামলা রুজু হওয়ার দিনদশেক পরে প্রথম খবর এল পার্ক স্ট্রিট থানায়।
‘খবর’ বলতে, একটা ইলেকট্রনিক গ্যাজেটস-এর দোকানে দু’জন অল্পবয়সি ছেলে এসেছিল ল্যাপটপ কিনতে। সঙ্গে কার্ড। কিন্তু কার্ড ‘সোয়াইপ’ করার পর দেখা যায়, কার্ডের নম্বরের সঙ্গে প্রিন্ট স্লিপের কিছু তফাত আছে। একটি ছেলেকে দোকানে বসিয়ে রাখা হয়েছে। অন্যজন? গেছে অন্য কার্ড আনতে।
থানা থেকে ‘ব্যাংক ফ্রড’ সেকশনে খরব আসতেই সঙ্গী অফিসারদের নিয়ে ছুটলেন সৌম্য। সুরাহা বোধহয় হয়েই গেল তদন্তের। আর সুরাহা! বছর বিশেকের যে ছেলেটি কাঁচুমাচু মুখে দোকানে বসে ছিল, তার নাম অঙ্কুশ তেওয়ারি। কলেজের গণ্ডি সবে ছাড়িয়েছে। বেকার। বাড়ি মানিকতলায়। আটক করা হল। জেরার পর্বটা তুলে রাখা হল লালবাজারে ফেরা পর্যন্ত। যে ছেলেটির অন্য কার্ড নিয়ে ফিরে আসার কথা, তার জন্য অপেক্ষা করা হল অনেকক্ষণ। কিন্তু সেই ছেলেটা সেই যে গেল, গেল তো গেল, আর এল না।
কে ছেলেটি? লালবাজারে রাতভর দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদে অঙ্কুশ জানাল, ছেলেটির সঙ্গে অল্প দিনেরই পরিচয়। নাম, মণিময় আগরওয়াল। আলাপ মিডলটন স্ট্রিটের এক চায়ের দোকানে। ছেলেটি দিনকয়েক আগে অঙ্কুশকে অনুরোধ করে, ‘তুই তো ভাই বেশ টেকস্যাভি, আমি একটা ল্যাপটপ কিনব ঠিক করেছি, দোকানে যাবি আমার সঙ্গে? স্পেসিফিকেশনগুলো জাস্ট বুঝিয়ে দিস কেনার সময়। যাতে ঠকে না যাই।’
—কোথায় থাকে মণিময়?
— ঠিকানা জানা নেই, তবে বলেছিল, আলিপুরের দিকে।
—মোবাইল নম্বর?
— মোবাইল আছে মণিময়ের, কিন্তু নম্বর জানি না।
—নম্বর জানা নেই মানে?
—সত্যি জানি না স্যার! আমার নিজের মোবাইল নেই। ওর মোবাইল নম্বর নেওয়ার দরকার পড়েনি সেভাবে।
উৎসাহিত হওয়ার মতো সূত্র একটাই। ড্রাইভিং লাইসেন্সে যে মহম্মদ সিকন্দরের ছবি ছিল, সেটা অঙ্কুশকে দেখানো হল। এবং অঙ্কুশ জানাল, এই ছবির সঙ্গে মণিময়ের মুখের প্রায় হুবহু মিল।
অঙ্কুশকে পরের দিন সকাল দশটা নাগাদ ছেড়ে দিলেন গোয়েন্দারা। কুড়ি বছরের ছেলেটি লালবাজারের গেট থেকে বেরিয়ে যখন হাঁটা দিল, জানতেও পারল না, সাদা পোশাকে দু’জন অফিসার নিঃশব্দে অনুসরণ করছেন নিরাপদ দূরত্ব থেকে। যাঁরা অবাক হয়ে লক্ষ করলেন, মানিকতলার বাসিন্দা অঙ্কুশ দক্ষিণ কলকাতাগামী মিনিবাসে উঠে বসলেন। নিমেষের মধ্যে একই বাসে সহযাত্রী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন দুই অফিসার।
পার্ক সার্কাসের কাছে নামল অঙ্কুশ। কিছুটা হেঁটে গিয়ে ঢুকল Ice Skating Rink–এর উলটোদিকের এক নামকরা কফিশপে। বেরিয়ে এল মিনিট পাঁচেকের মধ্যে। ফের হাঁটা দিল পার্ক সার্কাসের দিকে। এবং উঠে পড়ল উত্তরমুখী বাসে। কফিশপের সার্ভিস বয়ের সঙ্গে কথা বললেন অফিসাররা। অঙ্কুশ কিছুই অর্ডার করেনি। শুধু বলে গেছে, ‘আমার নাম অঙ্কুশ। আমার এক বন্ধুর একটু পরে এখানে আসার কথা। দু’জনে একসঙ্গে কফি খাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমার একটা জরুরি কাজ পড়ে যাওয়ায় পুলিশে যেতে হবে। বাড়িতে ক’দিন আগে একটা চুরি হয়ে গেছে। কেস হয়েছে। পুলিশ ডেকেছে লালবাজারে। তাই থাকতে পারছি না। কেউ এসে আমার নাম করে খোঁজ করলে বলে দেবেন, আমি আজ আর আসব না।’
আরও জানা গেল, অঙ্কুশ মাসে এক-দু’বার এখানে আসে কফি খেতে। কখনও একা, কখনও সঙ্গে দু’-তিনজন বন্ধু থাকে। এই বন্ধুদের মধ্যে একজন ছ’ফুটের উপর লম্বা নাইজেরিয়ানও আছে। যাকে ‘বেনসন’ বলে ডাকে অন্যরা। বেশিরভাগ সময় ফুটবলের জার্সি আর শর্টস পরেই আসত বেনসন। সার্ভিস বয় কথায় কথায় জানতে পেরেছিল, বেনসন ফুটবলার। কলকাতা ময়দানে খেলে।
এটুকু বোঝা যাচ্ছিল, অঙ্কুশকে যতটা চালাক ভাবা গিয়েছিল, বাস্তবে তার থেকে একটু বেশিই চতুর। কফির দোকানে যাওয়ার উদ্দেশ্য পরিষ্কার। তার বন্ধু বা বন্ধুদের কাছে ওই সার্ভিস বয়ের মাধ্যমে খবর পৌঁছনো, পুলিশ ‘ট্র্যাক’ করছে। সাবধান!
যে বন্ধুর সঙ্গে অঙ্কুশের কথা ছিল কফিশপে দেখা করার, সে কে? মণিময় আগরওয়াল, যে কার্ড বদলে আনছি বলে পার্ক স্ট্রিটের দোকান থেকে হাওয়া হয়ে গিয়েছিল? না কি অন্য কেউ? কেউ আসেনি অঙ্কুশের খোঁজে। কোনওভাবে খবর দিয়ে দিয়েছিল অঙ্কুশ বাড়ি ফেরার পথে? কোন পিসিও বুথ থেকে ফোন করে দিয়েছিল? কী-ই বা এমন কঠিন!
ডিসি ডিডি মিটিংয়ে বসলেন অফিসারদের নিয়ে। যা যা তথ্য হাতের কাছে ছিল, ঝালিয়ে নেওয়া হল।
এক, অঙ্কুশ ছেলেটা গোলমেলে। সেই জিজ্ঞাসাবাদের পরদিন থেকে মানিকতলার বাড়ি আর পাড়ার বাইরে বেরচ্ছেই না প্রায়। মোবাইল নেই বলে আরও মুশকিল। কার সঙ্গে কীভাবে কখন যোগাযোগ করছে, জানার উপায় নেই।
দুই, মণিময় চক্রের সঙ্গে যুক্ত, সন্দেহ নেই। কিন্তু খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ‘মহম্মদ সিকন্দর’-ই যে মণিময়, তা নিয়েও সংশয়ের জায়গা নেই। কফিশপের সার্ভিস বয় ছেলেটি বিহারি। লাইসেন্সের ছবি দেখে চিহ্নিত করেছে মণিময়কে। এবং জানিয়েছে, মণিময় তাকে বলেছিল, মল্লিকবাজারে তার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের কাপড়ের দোকান আছে। ছট পুজোর আগে সস্তায় জামাকাপড় কিনিয়ে দেবে।
সে না হয় হল, কিন্তু মল্লিকবাজারে অসংখ্য কাপড়ের দোকান। কোনটা মণিময়ের আত্মীয়ের, কী করে জানা যাবে? সিদ্ধান্ত হল মল্লিকবাজারে নজরদারির। জাল লাইসেন্সের ছবির প্রিন্টআউট সঙ্গে নিয়ে সোর্সরা মাঠে নামল।
তিন, বেনসন। নাইজেরীয় ফুটবলার। যাকে দ্রুত চিহ্নিত করা দরকার, কোথায় থাকে জানা দরকার। কী করে ফুটবল ছাড়া, জানতে হবে।
—স্যার, অঙ্কুশকে আরেকবার জিজ্ঞাসাবাদ করলে হয় না? সৌম্য প্রশ্ন করেন ডিসি ডিডিকে।
—করাই যায়। কিন্তু লাভ হবে কি কিছু? নতুন কিছু বেরবে? যেটুকু বলেছে, তার বেশি বলবে বলে মনে হয় না। আর যতটা বলেছে, তার থেকে খুব বেশি জানে তারও তো গ্যারান্টি নেই।
—হুঁ…
—একটু তলিয়ে ভাবো… অঙ্কুশ বা মণিময় জালিয়াতি চক্রের অংশ হতেই পারে, কিন্তু এই গ্যাং-এর শিকড় বিদেশে। কলকাতার দুটো ছেলের পক্ষে এই মাপের চক্র চালানো মুশকিল। এরা বড়জোর টিম মেম্বার। আসল পান্ডাদের খুঁজে বার করতে হবে। অঙ্কুশকে আর ডাকার দরকার নেই। ওকে ভাবতে দাও, ব্যাপারটা মিটে গেছে। কিন্তু চব্বিশ ঘণ্টা শ্যাডো করো। কী করছে, কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে দেখা করছে, সব…
—আর বেনসন?
—ওটা ইমপরট্যান্ট, ভেরি ইমপরট্যান্ট। ফরেন কানেকশন বলতে আপাতত বেনসনই। ওর সম্পর্কে খোঁজ নাও ডিটেলে। কোথায় থাকে, সেটা জানতে পারলে লোক বসিয়ে দাও বাড়ির সামনে। ওর মুভমেন্টের ব্যাপারেও রাউন্ড-দ্য-ক্লক রিপোর্ট জরুরি।
—ওকে আইডেন্টিফাই করাটা খুব সমস্যা হবে না স্যার। পেয়ে যাব মনে হয়। পেলে তুলে আনব লালবাজারে?
—নো। বাই নো মিনস। আমরা তো এখনও জানিই না ওর কতটা ইনভলমেন্ট। বা আদৌ ইনভলমেন্ট আছে কিনা। কিছু প্রমাণও নেই। কী হবে তুলে এনে? একটা কফিশপে অঙ্কুশ-মণিময়ের সঙ্গে সময় কাটায়। তো? হোয়াট ডাজ় দ্যাট প্রুভ?
—রাইট স্যার…
—জিজ্ঞেস করার মতো কিছু তো নেই এখনও। তারপরও ডাকলে উলটো ফল হবে। আমাদের ছেড়ে দিতে হবে ইন্টারোগেশনের পর। আর যদি সত্যিই ও এই চক্রের সদস্য হয়, তা হলে বেরিয়ে গিয়েই বাকিদের অ্যালার্ট করে দেবে। একটা ফোন, বা একটা ই-মেল, একটা টেক্সট মেসেজ়, ব্যস। আপাতত লোকটাকে ট্র্যাক করে ওর উপর নজরদারি চালানো ছাড়া কিছু করার নেই।
ট্র্যাক করার জন্য যা করণীয় ছিল, করলেন সৌম্য। ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (আইএফএ) অফিসে পরের দিন দুপর নাগাদ ঢুঁ মারলেন। নিজের পরিচয় গোপন রেখে।
নাইজেরিয়ান ফুটবলারদের লিস্ট পাওয়া যাবে? ফার্স্ট ডিভিশন, সেকেন্ড ডিভিশনের? চলতি মরশুম এবং তার আগের দু’-তিন বছরের?
আইএফএ-র কর্মকর্তা ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন নিস্পৃহ ভঙ্গিতে।
—কী দরকার? খেপ?
সৌম্য হাসেন অপ্রস্তুত।
—হ্যাঁ… মানে… কী করে বুঝলেন?
মধ্যবয়সি কর্মকর্তার ঠোঁটে একটা বিদ্রুপের হাসি খেলে যায়। যেন মাছকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, ভাই সাঁতার শিখলে কী করে?
—ফেব্রুয়ারিতে নাইজেরিয়ান প্লেয়ারের খোঁজ করতে একটা কারণেই লোক আসে।
—দাদা, আমরা আসলে একজন ভাল স্ট্রাইকারের খোঁজ করছিলাম। বেনসন বলে একটা ছেলে শুনেছি ভাল খেলছে ইদানীং। কিন্তু ঠিকানা জানি না। যদি একটু যোগাযোগ করা যায়… সে জন্যই…
—বেনসন? এবার সেকেন্ড ডিভিশনে খেলেছে ছেলেটা। অনেক গোল-টোল করেছে শুনেছি। পরের রার হয়তো ফার্স্ট ডিভিশনে টিম পেয়ে যাবে।
সৌম্য আড্ডা জমানোর চেষ্টা করেন।
—বড় টিম? মানে মোহনবাগান- ইস্টবেঙ্গল?
কর্মকর্তা ফের হাসেন। একটা সিগারেট ধরান।
—দুর মশাই। খেপেছেন? অত সোজা? সবাই কি চিমা ওকোরি বা এমেকা ইউজিগো নাকি? ছোট টিমগুলোও এখন বড় চেহারার বিদেশি খোঁজে। যারা অ্যাটাকিং থার্ডে গুঁতোগুঁতি করে গোলটা করে দেবে ঠিক সময়ে। অ্যাটাকিং থার্ড কাকে বলে জানেন তো?
সৌম্য মৃদু হাসেন। ফুটবল নিয়ে কর্মকর্তার কচকচি অসহ্য ঠেকলেও ধৈর্য হারান না। নিজে ভাল ফুটবল খেলতেন ছোট থেকেই। রাজ্য স্তরের ফুটবলে পুরুলিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। রাত জেগে ফলো করেন লা লিগা, ইপিএল-এর প্রতিটা ম্যাচ। মাঠটার প্রতিটা অর্ধ-কে যে তিনটে ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয়, ডিফেন্ডিং থার্ড, মিডল থার্ড আর অ্যাটাকিং থার্ড, এই কর্মকর্তার থেকে জানতে হবে?
—মোটামুটি জানি দাদা। তবে আপনার যা এক্সপিরিয়েন্স, আমরা তো নেহাতই বাচ্চা। বেনসনের একটা ছবি পাওয়া যাবে? মানে রেজিস্ট্রেশনের সময় ছবি তো দিতে হয়, সেখান থেকেই যদি… আর ঠিকানাটা…
—রেজিস্টার থেকে যা ছবি বেরয়, খুবই অস্পষ্ট। মুখাবয়ব পরিষ্কার করে বোঝার উপায় নেই। ঠিকানার জায়গায় লেখা আছে, ওয়াইএমসিএ হস্টেল, ধর্মতলা।
তবে ওই হস্টেলে না-ও পেতে পারেন। এরা কলকাতায় এসে সবাই ওখানেই প্রথমে ওঠে। তারপর একটু পয়সাকড়ি হাতে পেলে হয় একটা ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া করে নেয়। নয়তো ‘পেয়িং গেস্ট’ হয়ে থাকতে শুরু করে কোথাও।
—কিন্তু যোগাযোগ করব কী ভাবে? ধরুন ওয়াইএমসিএ–তে যদি না পাই…
কর্মকর্তা ভদ্রলোক এক মিনিট ভাবেন। সৌম্যর চোখমুখ দেখে বোধহয় একটু মায়াই হয়।
—সেক্ষেত্রে একটাই রাস্তা। মিল্টনদা।
—মিল্টনদা?
—হ্যাঁ, ময়দানের পুরনো লোক। মাঠই ধ্যানজ্ঞান। অফ সিজ়নে খেপ কে কোথায় খেলছে, কে কোথায় খেলবে, পুরোটা জানে। কন্ট্রোল করে। বাটা গ্রাউন্ডে সকাল থেকে পাবেন রোজ।
সঙ্গী অফিসারকে নিয়ে মিল্টনদার কাছে পৌঁছে গেলেন সৌম্য পরদিন সকালে। বেনসনের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবেন, আশ্বস্ত করলেন মিল্টন। দরদাম নিয়েও কথা হয়ে গেল।
—আপনি যখন বলছেন গোলটা ভাল চেনে, তখন না হয় পাঁচই দেব। ফাইনালটা জিততেই হবে যেভাবে হোক।
—আমি যখন বলছি মানে? পরশু একটা খেপ খেলতে যাবে। ইচ্ছে করলে গিয়ে দেখে নেবেন।
—কোথায় খেলা পরশু?
—হাওড়ায়। সাঁতরাগাছি পেরিয়ে।
.
সাঁতরাগাছি পেরিয়ে আরও বেশ কিছুটা। জায়গার নাম উনসানি। বেরতে একটু দেরিই হয়ে গিয়েছিল সৌম্য আর তাঁর সঙ্গীদের। তার উপর একটা গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়ে সাঁতরাগাছি ব্রিজ নট নড়নচড়ন। যখন গাড়ি গিয়ে মাঠের কাছাকাছি পৌঁছল, সেকেন্ড হাফ শেষ হতে বাকি মিনিট দশেক। ১-১। ম্যাচ শেষ হল ৩-১ স্কোরলাইনে। বেনসন দুটো গোল করল একাই। একটা হেডে। একটা গোলার মতো শটে। শেষ মুহূর্তে একটা শট বারে না লাগলে হ্যাটট্রিক হয়ে যায়। মিল্টন ভুল বলেননি। খেপ খেলায় এই বেনসনকে ম্যাচ পিছু পাঁচ হাজার দেওয়াই যায়।
টিমের বেশিরভাগ প্লেয়ার বাসে করে রওনা দিল কলকাতা। বেনসন চড়ে বসল একটা মারুতি ৮০০ গাড়ির পিছনের সিটে। খেপ-তারকার জন্য আলাদা ট্রিটমেন্ট। দ্বিতীয় হুগলি সেতু ধরে ছুটল মারুতি। পিছনে সামান্য দূরত্বে সৌম্যদের সাদা অ্যাম্বাসাডর।
বেনসনের গাড়ি যখন থামল তিলজলা এলাকার একটা একতলা ফ্ল্যাটের সামনে, সন্ধে নেমেছে কলকাতায়। সেই যে ফ্ল্যাটে ঢুকল, পরের দিন দুপুর অবধি বেরলই না বেনসন। নজরদারি চালু হল অষ্টপ্রহর। দেখা গেল রুটিন বলতে একটা মোটরবাইকে করে সকালে ময়দানে প্র্যাকটিসে যাওয়া আর মধ্য কলকাতার সদর স্ট্রিটে একটা ফ্ল্যাটে পেয়িং গেস্ট হিসেবে বসবাস। মাঝেমধ্যে নিশিযাপন তিলজলায় ওই ফ্ল্যাটে।
কার ফ্ল্যাট? লিন্ডা স্যামুয়েলস। মধ্য তিরিশের অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান যুবতী। সুন্দরী, বিবাহবিচ্ছিন্না। এক ছেলে, নাম সেবাস্তিয়ান। পড়ে মধ্য কলকাতার এক নামী কনভেন্ট স্কুলে। ক্লাস নাইন। লিন্ডা কাজ করেন বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের এক স্টিল কোম্পানির অফিসে। রিসেপশনিস্ট। বেনসন ছাড়াও দু’-একজন নাইজেরিয়ান যুবক মাঝেমাঝে আসে। এক কি দু’দিন থাকে। তারপর চলে যায়। এক মাঝবয়সি নাইজেরীয় অবশ্য মাস দুয়েক অন্তর অন্তর আসেন। আর এলে থাকেন অন্তত দু’সপ্তাহ। এক-দু’দিনের জন্য নয়।
অতঃকিম? বেনসনের খোঁজ পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে হদিশ মিলেছে মণিময়েরও। নজরদারিতে থাকা সোর্স খবর দিয়েছে, মণিময়কে দেখা গেছে মল্লিকবাজারে এক প্রৌঢ়ের দোকানে কিছুক্ষণ কাটাতে। কার দোকান? মহাবীর আগরওয়াল, মণিময়ের বাবা। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, মহাবীরের দুটো বিয়ে। থাকেন আলিপুরে। মণিময় দ্বিতীয় পক্ষের একমাত্র সন্তান। এবং এলাকায় এই বয়সেই চিটিংবাজ হিসেবে দুর্নাম কুড়িয়েছে। মোবাইল নম্বর? পাওয়া গেল। ফোন বন্ধ। শেষ টাওয়ার লোকেশন হরিদ্বার। বেশ, ঘাপটি মেরে আছে। থাক। আজ নয় কাল, ফিরতে তো হবেই কলকাতায়। যাবে কোথায়?
অঙ্কুশের কী খবর? মানিকতলার বাড়ি থেকে বেরচ্ছেই না প্রায়। লিন্ডার গতিবিধিতেও সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। বেনসনও আছে নিজের মতো।
লিন্ডার বাড়িতে রেইড করে লাভ নেই। একজন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলার একাধিক নাইজেরীয় বন্ধু থাকতেই পারে। তারা লিন্ডার ফ্ল্যাটে রাত কাটাতেই পারে। তাতে কী প্রমাণ হল? আসল ব্যাপার তো কার্ড স্কিমিং এবং তার নেপথ্যের চক্র। সেই চক্রের সঙ্গে এই বিদেশিদের জড়িত থাকার সম্ভাবনা আছে। সে থাকতেই পারে। কিন্তু আন্দাজের ভিত্তিতে কাউকে গ্রেফতার করা যায় না। আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে উলটো ফলই হবে। চক্রের চাঁই যে বা যারা, সে বা তারা সাবধান হয়ে যাবে।
আরেকটা মুশকিল, লিন্ডা মোবাইল ফোন ব্যবহার করেন না। ২০১০ সালে বেসরকারি সংস্থায় কর্মরতা মহিলার মোবাইল ফোন নেই, ভাবাই যায় না। কেন নেই? মোবাইল না নেওয়ার পিছনে কোনও বিশেষ কারণ? কারণ সে যা-ই হোক, এই বেনসন-টেনসনের মতো নাইজেরীয় বন্ধুরা যোগাযোগ করে কী করে লিন্ডার সঙ্গে? ল্যান্ডফোন? রেকর্ড দেখা হল। সন্দেহজনক কিছু নেই।
একটাই রাস্তা পড়ে থাকে যোগাযোগের। ই-মেল। লিন্ডার অফিস থেকে ই-মেল আইডি জোগাড় করতে অসুবিধে হল না। এবার জানা দরকার কার কার সঙ্গে কী কী মেল চালাচালি হয়। জানার উপায়? হ্যাকিং। তদন্তের প্রয়োজনে ততদিনে ‘ethical hacking’ শুরু হয়ে গিয়েছে কলকাতা সহ দেশের সর্বত্র। কয়েকজন তুখোড় হ্যাকারের সঙ্গে পুলিশের যোগাযোগ ছিলই। যাঁদের একজন লিন্ডার পাসওয়ার্ড ক্র্যাক করলেন মাত্র মিনিট পনেরোর মধ্যে।
আজকের দিনে পাসওয়ার্ড সুরক্ষিত রাখার ব্যাপারে আমি-আপনি অনেক সচেতন। সবাই জানি আমরা, অক্ষর-সংখ্যা-গাণিতিক চিহ্ন মিলিয়ে-টিলিয়ে একটা ভজঘট পাসওয়ার্ড তৈরি করা জরুরি। যেটা সহজে ভেদ করা যাবে না। সবাই জানেন, নিয়মিত পাসওয়ার্ড বদলানো দরকার। কিন্তু এ মামলা যখনকার, তখন সাইবার-সুরক্ষা বিষয়ে সচেতনতার মাত্রা ছিল অনেক কম।
লিন্ডাও ওই অসচেতনদের দলে পড়তেন। নিজের জন্মতারিখটা উলটে দিলে যা দাঁড়ায়, সেটা পাসওয়ার্ড হিসেবে রেখেছিলেন। যে তারিখটা লিন্ডার অফিস থেকে জানা হয়ে গিয়েছিল গোয়েন্দাদের। ‘চিচিংফাঁক’ হয়ে গেল লিন্ডার মেল।
গত কয়েক মাসের মেল ঘেঁটে বোঝা গেল, লিন্ডা পুরো ব্যাপারটা না-ই জানতে পারেন, কিন্তু তাঁর ফ্ল্যাটে যারা যাওয়া-আসা করে, তারা ধোয়া তুলসীপাতা নয়। পিটার বলে একজন প্রায়ই লিন্ডাকে নির্দেশ পাঠায় ই-মেলে। অমুক কাল কলকাতায় এক রাতের জন্য থেকে পরের দিন বাংলাদেশ যাবে, তাকে তোমার ফ্ল্যাটে থাকতে দিয়ো। তমুকের দিল্লিতে কিছু পুলিশি সমস্যা হয়েছে, আগামীকাল কলকাতায় যাবে। তোমার ফ্ল্যাটে রাতটা থাকবে। এইসব।
পিটারের মেলগুলোর প্রযুক্তিগত কাটাছেঁড়া করে জানা গেল, পাঠানো হয়েছে বিদেশ থেকে। কোন দেশ? নাইজেরিয়া!
হলই বা নাইজেরিয়া, কিন্তু জালিয়াতিতে জড়িত থাকার প্রমাণ? হয় কিছু প্রমাণ ছাড়া? হতাশ লাগছিল সৌম্যর। তা হলে কি এরা অন্য কোনও ধরনের বেআইনি কাজে যুক্ত? কার্ড স্কিমিং-এ নয়? কিন্তু আপাতত হাতে তো অন্য কোনও লিডও নেই, যে অন্য কোনও গ্যাং-এর খোঁজখবর করা যাবে। এ যা অবস্থা, শুধু পেনাল্টি বক্সের বাইরে পাসের দেওয়া-নেওয়াই চলছে। গোলের মুখ আর খোলা যাচ্ছে কই?
গোলের মুখ খোলার সামান্যতম আভাস মিলল দিনকয়েক পর। রোজই পিটার-লিন্ডার মেল চালাচালিতে চোখ রাখতেন সৌম্য। এক রাতে নিয়মমাফিক ‘হাই-হ্যালো-লাভ ইউ ডিয়ার’-এর পাশাপাশি পিটারের তরফে একটা মেল, ‘Please keep Mr.Stanley Rodrigues safe.’
মানে? Stanley Rodrigues-টা আবার কে? এ তো নতুন মোচড় তদন্তে। যাকে বলে, ‘কাহানি মে টুইস্ট’! কে স্ট্যানলি? সেই মাঝবয়সি, যে দু’মাস অন্তর আসে আর লিন্ডার ফ্ল্যাটে থাকে বেশ কিছুদিন? তা হলে স্ট্যানলিই কি নাটের গুরু? লিন্ডাকে মেল করে স্ট্যানলিকে ‘সেফ’ রাখতে বলছে কেন পিটার? ‘সেফ’ রাখার প্রয়োজন পড়ছে কেন? কী সম্পর্ক স্ট্যানলির সঙ্গে পিটারের? রাখতেই যদি হয়, স্ট্যানলিকে কোথায় ‘সেফ রাখবেন লিন্ডা? এই ফ্ল্যাট ছাড়া অন্য গোপন আস্তানা আছে মহিলার? নজরদারি তো সমানে চলছে। অফিস-বাড়ি আর রোববারে চার্চ, এর বাইরে তো কোথাও যান না মহিলা। বেনসন ছাড়া আর যে নাইজেরীয়রা মাঝেমধ্যে লিন্ডার ফ্ল্যাটে আসে, তাদের মধ্যে কারও কথা বলছে? যদি তা-ই হয়, ঝুঁকি নিয়ে লিন্ডার বাড়িতে রেইড করতে হয়। আর করলেও তখন এই স্ট্যানলি থাকবে, কী গ্যারান্টি? বরং খুঁচিয়ে ঘা করলে হয়তো স্ট্যানলি, যাকে পিটার নিরাপদে রাখার নির্দেশ দিয়েছে লিন্ডাকে, আর এ তল্লাট মাড়ালই না। তখন?
‘তখন’ যে পুরো গ্যাংটাই হাতের বাইরে চলে যেতে পারে, সেটা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না গোয়েন্দাদের। আরও একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হচ্ছিল। এসব মামলায় ‘ডিজিটাল এভিডেন্স’ সংগ্রহ না করতে পারলে চার্জশিটটা দাঁড়াবেই না। আর সাইবার-ফুটপ্রিন্টস মুছে ফেলতে আর কতক্ষণ? সাবধানে পা ফেলা ছাড়া উপায় কী?
স্ট্যানলির খোঁজে ফের যাওয়া হল আইএফএ অফিসে। এই নামে কোনও নাইজেরীয় ফুটবলার আছে? নেই। নাইজেরীয় দূতাবাসে নেওয়া হল খোঁজখবর। এই নামের কেউ ভারতে এসেছেন সম্প্রতি? কোনও রেকর্ড আছে? পাওয়া গেল না। শহরের যেখানে যেখানে নাইজেরীয়দের বেশি দেখা যায়, সোর্স লাগানো হল সেখানে। স্ট্যানলি নামের কারও খোঁজ পেলেই যেন খবর পাওয়া যায়। সপ্তাহ পেরিয়ে গেল, খবর এল না কিছু।
কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। এবং ক্রেডিট কার্ড জালিয়াতির আরও টুকটাক অভিযোগ জমা পড়ছে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই। অথচ তদন্তে যা যা করার, সবই তো করা হচ্ছে। মার্চের মাঝামাঝি একদিন কাজ সেরে অফিস থেকে যখন বেরচ্ছেন হতোদ্যম সৌম্য, রাতের লালবাজার শুনশান। বোসপুকুরে নিজের ফ্ল্যাটে পৌঁছতে পৌঁছতে মাঝরাত হয়ে গেল সৌম্যর। ড্রয়িংরুমের সেন্টারটেবিলে ‘ফেলুদাসমগ্র’ রাখা। একমাত্র কন্যা ক্লাস সিক্সে পড়ে। গোয়েন্দাগল্পের পোকা। ফেলুদা বলতে অজ্ঞান। অবশ্য কে নয়? সময়-সুযোগ পেলে সৌম্য নিজেই পঞ্চাশবার পড়া ফেলুদা-কাহিনি আবার নিয়ে বসে যান পাতা উলটোতে। বইটায় বুকমার্ক দিয়ে শুতে গেছে মেয়ে। সৌম্য হাতে তুলে নেন। শোবার আগে ‘ঘুরঘুটিয়ার ঘটনা’ পড়ছিল। গল্পটার নাম শুনলেই অবধারিত মনে পড়ে যায় কালীকিঙ্করবাবুর সেই টিয়ার কথা, ‘ত্রিনয়ন ও ত্রিনয়ন একটু জিরো’। সিন্দুকের কম্বিনেশন লকের কোড। ফেলুদার মগজাস্ত্র যে কোডের রহস্যভেদ করেছিল, ‘থ্রি নাইন জিরো থ্রি নাইন এইট টু জিরো!’
ঘুম আসতে দেরি হবে আজ। মাথায় ঘুরছে Mr Stanley Rodriges। ফেলুদার বই রেখে দিয়ে লম্বা শ্বাস ফেলেন সৌম্য। মগজাস্ত্রের প্রয়োগ যদি করা যেত ফেলু মিত্তিরের মতো! বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে একসময় উঠে পড়েন। কম্পিউটার খুলে বসেন। শূন্য থেকে শুরু করা যাক। কার্ড স্কিমিং-এর জালিয়াতি বিশ্বের কোথায় কোথায় কীভাবে হয়েছে, কীভাবে সমাধান হয়েছে, লিঙ্কগুলো আবার দেখা যাক। যদি দিশা পাওয়া যায় কিছু।
গুগল নিমেষে লিঙ্ক ভাসিয়ে দিল অসংখ্য। সৌম্য চোখ বোলাচ্ছিলেন। একটার হেডিং, ‘All you need to know about MSR’। এটা আগেও পড়েছিলেন। MSR, অর্থাৎ ‘Magnetic Stripe Readers’। দেখতে থাকেন সাব-হেডিং, “how to keep your card safe from MSR”.. ‘Magnetic Stripe Reader, a device used to read magnetic stripe cards such as credit cards.’
একবার পড়েন, দু’বার পড়েন। বারবার তিনবার পড়েন। তৃতীয় বারের পড়ায় শুধু দুটো শব্দে চোখ চুম্বকের মতো আটকে যায়। ‘Safe’ আর ‘MSR’। কেন চোখ সরছে না? কেন স্নায়ু আচমকাই চঞ্চল হয়ে উঠছে? কেন মস্তিষ্কে উত্তেজক তরঙ্গ টের পাচ্ছেন হঠাৎ?
সংকেত? কোড? ‘ত্রিনয়ন ও ত্রিনয়ন’ -এর মতো? M ফর Mr, S ফর Stanley, R ফর Rodrigues? MSR? যাকে ‘safe’ রাখতে সাংকেতিক নির্দেশ পাঠিয়েছে পিটার? হতেই হবে.. এটা কোডই … কোড না হয়ে যায় না… Magnetic Stripe Reader? এ ছাড়া আর কোনও সম্ভাবনা পড়ে থাকে না। সৌম্য বুঝতে পারেন, রাতে ঘুম আসবেই না আর। ফোনে ধরেন ওসি ব্যাংক ফ্রড-কে, ‘স্যার, Mr. Stanley Rodrigues…!’
.
লিন্ডার বাড়িতে এখন ‘রেইড’ করাটা মূর্খামি হবে, সিদ্ধান্ত হল সর্বসম্মত। MSR পাওয়া গেলেও পিটারকে আর পাওয়া যাবে না। দিন পনেরোর মধ্যেই যে কলকাতায় আসবে বলে লিন্ডাকে জানিয়েছে মেলে। ঘটনার বিশ্লেষণ করে যা বোঝা যাচ্ছে, পিটার অন্যতম নাটের গুরু। এখন আছে নাইজেরিয়ায়। লিন্ডার ভাড়ার ফ্ল্যাটটা তার কলকাতার আস্তানা। বেনসন-মণিময়-অঙ্কুশরা, যেমন ভাবা গিয়েছিল, স্রেফ চুনোপুঁটি স্তরের শাগরেদ।
অপেক্ষা করা শুরু হল পিটারের শহরে আসার। বেনসনের খেলাধুলো আর লিন্ডার বাড়ি আসা-যাওয়া স্বাভাবিকভাবেই চলছে। অঙ্কুশও আর আগের মতো ঘরবন্দি থাকছে না। এবং যেমন ভাবা হয়েছিল, পুলিশি খোঁজখবর একটু থিতিয়ে যেতেই কলকাতায় ফিরে এসেছে মণিময়। মেট্রোপ্লাজার একতলার একটা রেডিমেড কাপড়ের দোকানে বসছে নিয়মিত। এদের ধরা তো জলভাত। ঠিক সময়ে তুলে নেওয়া যাবে।
অবশেষে লিন্ডার ইনবক্সে ঢুকল কাঙ্ক্ষিত বার্তা। ‘Sweetheart, arriving tomorrow…’। লাগোস থেকে দুবাই হয়ে কলকাতায় আসছে পিটার। এমিরেটস-এর ফ্লাইটে।
তিনটে টিম করা হল। একটা যাবে এয়ারপোর্টে, পিটারকে ধরতে। একটা কিড স্ট্রিটের ডেরা থেকে বেনসনকে তুলবে। আর তৃতীয় দলের দায়িত্ব থাকবে অঙ্কুশ-মণিময়কে তুলে আনার।
এর পরের ঘটনাপ্রবাহ শুরুর অনুচ্ছেদে লিখেছি। এয়ারপোর্ট থেকে বেরনোর পর লিন্ডা পিটারকে জড়িয়ে ধরা মাত্র ঘিরে ধরলেন অফিসাররা।
—ইয়োর গেম ইজ় আপ…
—হোয়াট? হোয়াট গেম আর ইউ টকিং অ্যাবাউট? আই ডোন্ট গেট দিস…
.
স্বীকারোক্তি আদায়ে বিশেষ অসুবিধে হল না। লিন্ডা আর পিটারকে একসঙ্গে বসিয়ে মেল চালাচালির প্রিন্ট আউটগুলো মেলে ধরা হল সামনে। তার আগেই পিটারের ব্যাগ থেকে উদ্ধার হয়েছে বিভিন্ন নামের গোছা গোছা কার্ড। পিটার-লিন্ডা কবুল করলেন দ্রুত, হ্যাঁ, Mr. Stanley Rodrigues আসলে ‘Magnetic Stripe Reader’–এর সংকেতই। লিন্ডার বাড়ির উদ্দেশে রওনা দিল টিম, আলমারির মধ্যে থেকে উদ্ধার হল MSR 205 মেশিনটি। যা দিয়ে তৈরি করা হত জাল কার্ড।
বেনসনের কাছ থেকেও পাওয়া গেল বেশ কয়েক গোছা জাল কার্ড। এবং তার পাসপোর্টটা ভাল করে দেখার পর বোঝা গেল, ভারতে থাকার ভিসার কাগজটাও জাল।
পিটারের ব্যাগ থেকে একটা ল্যাপটপ পাওয়া গেল। সেটা বাজেয়াপ্ত করার আগে ডেটা কপি করে নেওয়া হল একটা হার্ড ডিস্কে। ডিস্কটার আদ্যোপান্ত ঘেঁটে দেখা গেল, পিটার মার্কিন নাগরিকদের কার্ডের তথ্য পেত একটা মেল আইডি থেকে। man-t-2@yahoo.com। কথাবার্তা হত yahoo messenger-এ।
কে এই man-t-2? পিটার জানাল, man-t-2-র নাম জেমস। নাইজেরীয়, ভারতেই থাকে। একসময় আমেরিকাতে ছিল। মার্কিন বন্ধুবান্ধব আছে বেশ কিছু। তা হলে আসল লোক পিটার নয়, জেমস?
Yahoo Messenger-এর লগ ডিটেলস নিয়ে বিস্তর ঘাঁটাঘাঁটি করে বোঝা গেল, জেমসের বর্তমান অবস্থান পুনেতে। ভোঁসারি থানার অন্তর্গত গণেশওয়াড়ি নামের এক জায়গায়। অতএব চলো পুনে।
.
গণেশওয়াড়ি। মহল্লার আয়তন ছোট নয় খুব একটা। দিনভর এলাকা চষে ফেললেন সৌম্য এবং সহযোগী অফিসাররা। দোকানে-পাড়ায়-রকের আড্ডায় স্থানীয়দের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে জানার চেষ্টা করলেন, কালো চামড়ার লোক থাকে নাকি আশেপাশে? সন্ধের দিকে এক চায়ের দোকানের মালিকের কাছে হদিশ মিলল।
—আপনারা কি কালো ইংরেজদের কথা জিজ্ঞেস করছেন।
—হ্যাঁ হ্যাঁ, গায়ের চামড়া কালো, কিন্তু ইংরেজিতে কথা বলে? জানেন?
—হ্যাঁ, কালো ইংরেজ থাকে একটা বাড়িতে। এই রাস্তাটা ধরে সোজা গিয়ে একটা মোড় পড়বে, সেখান থেকে বাঁ দিকে…
—একটু দেখিয়ে দিন না প্লিজ়… সেই কলকাতা থেকে এসেছি।
দেখিয়ে দিলেন চা-দোকানি। সঙ্গে সঙ্গে সৌম্য যোগাযোগ করলেন ভোঁসারি থানায়। ‘রেইড’ করা হল প্রায় মাঝরাতে। বেল বাজানোর পর দরজা খুললেন স্কার্ট-টপ পরিহিতা এক তরুণী। ভারতীয়। যিনি কিছু বোঝার আগেই হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়ল পুলিশ। এবং দু’কামরার ছিমছাম ফ্ল্যাটের শোওয়ার ঘরে আবিষ্কার করল এক নাইজেরীয় তরুণকে। টি-শার্ট আর শর্টস পরে একমনে ঝুঁকে ল্যাপটপের স্ক্রিনে।
পিঠে হাত পড়তে মুখ তুলে তাকালেন তরুণ। সৌম্য সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন, ‘How is life James?’
—I am not James. Myself Christopher.
—And who is she?
—She’s Noa. Lives in Chennai. We are going to be married soon and shall leave for Dubai.
পাসপোর্ট দেখালেন যুবক। নাম সত্যিই ক্রিস্টোফার। নোয়া নামক তরুণীকে বিয়ে করে পাড়ি দেওয়ার কথা দুবাই। ভিসাও হয়ে গেছে। কাগজপত্র দেখা হল। মিথ্যে নয়। পাসপোর্ট-ভিসায় গরমিল নেই কোনও। তা হলে?
‘জেমস’ শব্দটা উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে যে নোয়ার মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল আচমকা, লক্ষ করেছিলেন এক অফিসার। কেন, সেটা বোঝা গেল বসার ঘরে পড়ে থাকা একটা চামড়ার ব্যাগ তল্লাশি করার পরেই। যাতে পাওয়া গেল বেশ কিছু জামাকাপড় আর কিছু ফটো। ছবিতে দেখা যাচ্ছে এক মাঝবয়সি নাইজেরীয়কে। এই ক্রিস্টোফারের সঙ্গে কোনও মিল নেই ছবির।
—ফটোর লোকটা কে? এক মহিলা অফিসারের ধমকে নোয়া ভেঙে পড়লেন।
—জেমস। তোমরা যাকে খুঁজছ। Egbe Dakun James Taino। এই ফ্ল্যাটটা ওর ভাড়া করা। ক্রিস্টোফার ওর বন্ধু। ক্রিস্টোফার আর আমাকে এখানে থাকতে দিয়েছে জেমস। আজ বিকেলের ফ্লাইটে মুম্বই হয়ে দিল্লি গেছে। তবে কয়েকদিন পরই ফিরবে। আমরা এর বেশি কিছু জানি না স্যার।
শর্ত দিলেন সৌম্য। দুবাইও যাওয়া হবে, আর বিয়েও ভণ্ডুল হয়ে যাবে না, যদি জেমস এই ফ্ল্যাটে ফেরার পর ওঁরা ফোন করে জানিয়ে দেন কলকাতায়। আপাতত ওঁদের পাসপোর্টগুলো জমা রইল পুলিশের কাছে। জেমসের খবর পেলে পুলিশ আবার আসবে। তখনই ফেরত দেওয়া হবে পাসপোর্ট।
প্রস্তাবে রাজি না হয়ে উপায় ছিল না ওঁদের। সৌম্যরা ফিরে এলেন কলকাতায়। ভোঁসারি থানার অফিসাররা নজরদারির ব্যবস্থা করলেন ফ্ল্যাটে।
বহুপ্রতীক্ষিত ফোন এল দিনদশেক পরে। সাতসকালে সৌম্যর মোবাইলের স্ক্রিনে ভেসে উঠল, ‘Noa Calling’।
—স্যার, জেমস গত কাল রাতে এসেছে। ঘুমচ্ছে এখন। কাল সকালের ফ্লাইটে আবার মুম্বই চলে যাবে।
মানে দাঁড়াচ্ছে, আজই পৌঁছতে হবে, যে ভাবেই হোক। তদন্তে এমন হয় কখনও কখনও, এক সেকেন্ডও দেরি করা চলে না। যেটা করতে হবে, সেটা তখনই করতে হবে।
করা হল। গোয়েন্দাপ্রধানকে জানানো হল। যাঁর নির্দেশে দুপুরের ফ্লাইটে মুম্বই রওনা দিলেন অফিসারেরা। মুম্বই-পুনে হাইওয়ে ধরে রওনা দিলেন সড়কপথে। যখন গণেশওয়াড়ি পৌঁছনো গেল, ঘড়ির কাঁটা সাড়ে আটটা ছাড়িয়ে ন’টার পথে রওনা দিয়েছে।
মাঝবয়সি নাইজেরীয়, James Taino, Yahoo messenger-এ চ্যাট করছিলেন ফ্ল্যাটে বসে। আইডি? man-t-2।
ল্যাপটপের দু’-একটা ফোল্ডার এলোমেলো চেক করতেই বেরিয়ে পড়ল অজস্র কার্ডের ডিটেলস। Track-1 এবং Track-2, যেগুলো থাকে কার্ডের পিছনের ম্যাগনেটিক স্ট্রিপের মধ্যে। খালি চোখে যা দেখতে পাওয়ার কথাই নয়। ডেটা বোঝাই হয়ে আছে ল্যাপটপে। যা দিয়ে চলছিল লক্ষ লক্ষ টাকার জালিয়াতি, ‘ইধার কা মাল উধার’।
পরের দিন জেমসকে স্থানীয় কোর্টে হাজির করে ‘Transit Remand’ নিয়ে ফের রওনা দেওয়া। সড়কপথে ফের মুম্বই। সেখান থেকে কলকাতার উড়ান।
.
অঙ্কুশ-মণিময়-লিন্ডা রাজসাক্ষী হয়েছিলেন। পুরো ঘটনা স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছিলেন বিচারকের সামনে। জানিয়েছিলেন, তাঁরা স্রেফ বোড়ে ছিলেন, জানতেন না কিস্তিমাতের আসল ছক। লিন্ডা অকপটে বলেছিলেন আদালতে, জেমসের সঙ্গে আলাপ মধ্য কলকাতার এক চার্চে। জড়িয়ে পড়েছিলেন গভীর সম্পর্কে। যা বলতেন জেমস, অন্ধের মতো মেনে চলতেন।
জেমসের থেকে পাওয়া গেল আমেরিকা-প্রবাসী দুই নাইজেরীয় বন্ধুর খুঁটিনাটি। যারা সরবরাহ করত কার্ডের তথ্য। এবং জেমস ভারতে বসে লোপাট করে দিত লক্ষ লক্ষ টাকা। ভাগবাঁটোয়ারা হত অনলাইনে। FBI (ফেডারাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন)-এ বিস্তারিত জানিয়ে মেল করে দেওয়া হল লালবাজারের তরফে।
তিন বছর লেগেছিল বিচারপর্ব শেষ হতে। রাজসাক্ষী লিন্ডা-অঙ্কুশ-মণিময়কে সাজা দেননি আদালত। দশ বছরের কারাদণ্ড বরাদ্দ হয়েছিল তিন চক্রীর জন্য। বেনসন-জেমস-পিটার।
শাস্তি যেদিন ঘোষণা হয়েছিল, আদালত থেকে বেরনো মাত্রই ফোনে মেসেজ এসেছিল সৌম্যর। ডিসি ডিডি লিখেছিলেন, ‘Well done. The reward of a good job done is to have done it.’
সেই মেসেজ আজও যত্ন করে রেখে দিয়েছেন সৌম্য। ভাল কাজের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার কী হতে পারে? ভাল কাজটাই তো!
পুনশ্চ: লিন্ডা, অঙ্কুশ এবং মণিময়, তিনটি নাম পরিবর্তিত ওঁদের সামাজিক বিড়ম্বনা এড়াতে।
২.১১ দ্য পারফেক্ট ক্রাইম
[স্টোনম্যান
বারোটি মামলায় একাধিক তদন্তকারী অফিসার ছিলেন।]
ক্রিং ক্রিং…
কাঁচা ঘুম ভেঙে গেলে যা হয়, মেজাজটা খিঁচড়ে গেল গোয়েন্দাপ্রধানের। অনেক রাত অবধি একটা কেস ডায়েরি দেখেছেন। ডাকাতির মামলা। ঘটনার সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ধরা পড়ে গিয়েছিল ডাকাতরা। তথ্যপ্রমাণ জোগাড় করে আড়াই মাসের মধ্যেই তদন্তকারী অফিসার চার্জশিট তৈরি করে ফেলেছেন বিস্তর খেটেখুটে। কাল-পরশুর মধ্যেই জমা পড়বে আদালতে। কোথাও কোনও ফাঁকফোকর যাতে না থাকে, একবার তাই খুঁটিয়ে দেখতেই হত। ফাইলটা বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। ডিনারের পরে বসেছিলেন কেসটা নিয়ে। চার্জশিটের খুচরো ভুলগুলো লাল পেনে মার্ক করে যখন শুতে গিয়েছিলেন, ঘড়ির কাঁটা দুটো ছাড়িয়েছে। জমাট ঘুমের মধ্যপথে ছন্দপতন পৌনে পাঁচটা নাগাদ ..ক্রিং ক্রিং..।
কথায় বলে, ভোরের স্বপ্ন নাকি সত্যি হয়, সে ভাল হোক বা মন্দ। ভোরের স্বপ্নের সত্যি-মিথ্যে জানা নেই। তবে পুলিশের চাকরিতে কাকভোরের ফোন অশনিসংকেতই বয়ে আনে সচরাচর। দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর কেউ ভোরে সিনিয়র অফিসারের ঘুম ভাঙাতে বাধ্য হচ্ছে মানে, অবধারিত কোথাও ডাকাতি, নয়তো খুন। কিংবা দাঙ্গা, বা আরও খারাপ কিছু। ঘুমচোখেই বেডসাইড টেবলে রাখা ফোনের রিসিভারটা তুললেন গোয়েন্দাপ্রধান। অন্য প্রান্ত থেকে যে উদ্বিগ্ন আওয়াজটা ভেসে এল, সেটা দীর্ঘদিনের পরিচিত। ওসি হোমিসাইড।
—নমস্কার স্যার, আবার!
আবার! শুনেই বিছানা ছেড়ে উঠে বসেন গোয়েন্দাপ্রধান।
—মানে?
—আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজের কাছে স্যার.. সিইএসসি-র ট্রান্সফর্মার আছে একটা …
—কখন হল?
—খবরটা থানায় এসেছে মিনিট দশেক হল, আমি থানার ফোনটা পেয়েই…
—তুমি শিয়োর? আই মিন মোডাস অপারেন্ডি…
—হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্যার.. যা শুনলাম .. জাস্ট দ্য সেম..
—হুঁ .. তোমরা বেরও.. পৌঁছও অ্যাজ় আর্লি অ্যাজ় পসিবল..আসছি।
ফোনটা কেটে দেওয়ার পর মিনিটখানেক থম মেরে বসে থাকেন গোয়েন্দাপ্রধান। আবার? তা হলে যে অস্বস্তিটা কাঁটা হয়ে বিঁধছিল মাসখানেক ধরে, সেটাই সত্যি হল? ইংরেজিতে বলে না.. ‘worst fears coming true?’
সিপি-কে এখনই জানানো দরকার। বেরনোর জন্য তৈরি হতে হতেই ফোনে ধরলেন। সিপি শুনলেন এবং একটিই শব্দ খরচ করলেন, ওসি হোমিসাইডের একটু আগের ফোনে ‘নমস্কার স্যার’-এর পর যে শব্দটা ছিটকে এসেছিল।
—আবার!
গোয়েন্দাপ্রধানের গাড়ি যখন মৌলালির কাছাকাছি, আলো আলতো আঁচড় কাটতে শুরু করেছে আকাশে। রাত তখন ভোরপ্রবণ।
.
—স্যার, সুভাষবাবুর পরের সভাটা কখন কোথায়, বলবেন প্লিজ়?
সুদূরতম কল্পনাতেও উলটোদিকের চেয়ারে বসে থাকা মাঝবয়সি লোকটির থেকে এ প্রশ্ন আশা করেননি ওসি হোমিসাইড। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকেন যুবকের মুখের দিকে। ভুল শুনলেন না তো? জিজ্ঞেস করেন ঠান্ডা গলায়, ‘কার সভা?’
উত্তর আসে নির্বিকার।
—সুভাষবাবুর স্যার, নেতাজি সুভাষ।
মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন গোয়েন্দারা। ইয়ার্কি করছে? লালবাজারে এসে মশকরা করবে, তা-ও হাতেনাতে ধরা পড়ার পর? না কি সেয়ানা পাগলের ভেক ধরেছে মার এড়াতে?
এক অফিসার কলার চেপে ধরেন মাঝবয়সির।
—চ্যাংড়ামি হচ্ছে? ইয়ার্কি মারার জায়গা পাননি? নেতাজি? সোজাসুজি সবটা খুলে বলুন, একটা একটা করে। আদরযত্ন তো এখনও শুরুই করিনি। শুরু করলে একটা মারও বাইরে পড়বে না, গলগল করে বেরিয়ে আসবে সব। যত্নআত্তি করব, না এমনিই বলবেন? ব্যাটা বলে কিনা সুভাষবাবু!
অবাক হয়ে অফিসাররা লক্ষ করেন, কোনও ভাবান্তর নেই লোকটির। শরীরী নড়াচড়ায় না আছে কোনও উদ্বেগের আভাস, না আতঙ্কের। মৃদু হেসে জবাব দেয় পুলিশি হুমকির, ‘হ্যাঁ স্যার, নেতাজি। কী অপূর্ব বললেন আজ! বললেন, ‘তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব! মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনলাম। গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। পরের সভাটা কোথায় হবে স্যার?’
ধৈর্য বিপদসীমা অতিক্রম করে ওসি হোমিসাইডের। হাড়মাস কালি হয়ে গেছে এই লোকটার জন্য। চাকরিটাই যেতে বসেছিল প্রায়। আর ধরা পড়ার পর টাইমমেশিনে নেতাজির আমলে ফিরে যাওয়ার অভিনয় করে চলেছে আধঘণ্টা ধরে। এখনই একটি প্রবল চপেটাঘাত প্রয়োজন। এমন একটি বিরাশি সিক্কা, যা দ্রুত বর্তমানে ফিরিয়ে আনবে শ্ৰীমানকে।
থাপ্পড়টা অসমাপ্তই থেকে যায় গোয়েন্দাপ্রধানের হন্তদন্ত আবির্ভাবে। যিনি খবর পেয়েই ছুটে এসেছেন পড়িমরি। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান ওসি, ‘আসুন স্যার.. বসুন..।’
বসেন না গোয়েন্দাপ্রধান। একদৃষ্টে স্থির তাকিয়ে থাকেন চেয়ারে বসা স্মিতহাস্য লোকটির দিকে। এই লোকটা? এ-ই স্টোনম্যান? যে শুধু লালবাজার নয়, পুরো শহরের ঘুম কেড়ে নিয়েছে গত ন’মাস ধরে? শান্তভাবে প্রশ্ন করেন মাঝবয়সিকে, ‘কী নাম আপনার?’
.
ফিরে দেখা সেই মামলাকে, প্রায় তিন দশক পেরিয়েও যা নিয়ে আমজনতার ঔৎসুক্যের পারদ কণামাত্র নিম্নগামী হয়নি, কৌতূহলের তীব্রতার নিরিখে যা কলকাতা পুলিশের শতাব্দীপ্রাচীন ইতিহাসে আজও তর্কাতীত শীর্ষবাছাই।
১৯৮৯-এর চৌঠা জুনের সাতসকাল। হেয়ার স্ট্রিট থানার ডিউটি অফিসার ফোনটা ধরলেন, শুনলেন এবং বুঝলেন, দিনটা খারাপ ভাবে শুরু হতে যাচ্ছে। খুন হয়ে গেছে একটা। কোথায়? লালবাজারের নাকের ডগায়।
‘নাকের ডগা’ বলতে বিবাদী বাগের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনা। মধ্যতিরিশের মহিলা পড়ে আছেন প্রাণহীন। গভীর ক্ষতচিহ্ন মৃতার মাথার ডান দিকে। মাথার পাশেই পড়ে রয়েছে একটা বড় পাথর। যাতে রক্তের লাল-কালচে ছিটে জানান দিচ্ছে, খুনির হাতিয়ার ছিল ওই পাথরটাই। যার ওজন প্রায় সাড়ে নয় কেজির মতো। ফরেনসিক পরীক্ষা ছাড়াই বোঝা যাচ্ছিল সাদা চোখে, একেবারে কাছ থেকে খুনি পাথরটা আছড়ে ফেলেছে মহিলার মাথায়। অত ভারী পাথর মাথায় সজোরে আঘাত করলে যা হয়, ঘুমের মধ্যেই মৃত্যু এসেছে অনিবার্য। ডাক্তারি পরিভাষায়, ‘Death was due to the effects of injuries, ante-mortem and homicidal in nature.’
মৃতার পরিচয়? আলেয়া বিবি, ফুটপাথবাসিনী। স্থায়ী আস্তানা বলতে কিছু ছিল না। স্বামী মোহন সাউয়ের খুচরো বিক্রিবাটার কাজে টুকটাক সাহায্য করতেন। রাস্তাতেই দম্পতির দিন গুজরান, রাস্তাতেই নিশিযাপন। রাত এগারোটা নাগাদ ঘুমিয়েছিলেন রোজকার মতো। ভোরে আবিষ্কৃত হল মৃতদেহ। পোস্টমর্টেম রিপোর্ট জানাল, খুনটা হয়েছে রাত চারটে থেকে সাড়ে চারটের মধ্যে। শরীরের অন্য কোথাও কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই, চিহ্ন নেই কোনওরকম বলপ্রয়োগের। মৃতা তিন মাসের সন্তানসম্ভবা ছিলেন।
কে খুনটা করল-র থেকেও ‘কেন করল’-টাই ধন্দে ফেলল হোমিসাইড শাখার গোয়েন্দাদের। মোহন সাউ স্ত্রী আলেয়াকে নিয়ে বিহারের দ্বারভাঙা থেকে জীবিকার খোঁজে কলকাতায় এসেছিলেন কয়েক বছর আগে। দিন আনি দিন খাই-এর চালচুলোহীন সংসার। ঠিকানা ফুটপাথ। আলেয়াকে খুন করে অর্থলাভের সম্ভাবনা শূন্য। মোটিভ হিসাবে অন্য যে সম্ভাবনাটা মাথায় আসবেই, যৌন-ঈর্ষা? স্বামী-স্ত্রী-র সম্পর্কে কোনও তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাবজনিত টানাপোড়েন? খোঁজখবর নেওয়া হল যতটা তলিয়ে সম্ভব, কিন্তু মোহন-আলেয়ার সম্পর্কে ন্যূনতম অশান্তি-অস্থিরতার আঁচ পাওয়া গেল না। তা হলে?
‘তা হলে?’-র উত্তর অমিলই থাকল প্রায় মাসদেড়েক। তার পরেও যে ধাঁধার জবাব পাওয়া গেল, এমন নয়। বরং ঘটল উলটোটা। ১৯ জুলাইয়ের রাত রাতারাতি অন্য মাত্রা দিল পঁয়তাল্লিশ দিন আগের আলেয়া-হত্যাকে, যাকে স্রেফ একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত করার বিলাসিতা আর রইল না লালবাজারের। থাকবেই বা কী করে? এবার তো জোড়া খুন!
প্রথমটা তালতলা থানা এলাকায়। জিয়োলজিকাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া-র উত্তরমুখী গেটের অদূরে, পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনে ঢোকার সিঁড়ির মুখে। চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছরের নিথর রক্তাক্ত দেহটা ছ’টা-সোয়া ছ’টা নাগাদ নজরে আসে পথচারীদের। ছেঁড়াখোঁড়া জামাপ্যান্ট, শীর্ণ চেহারায় অপুষ্টির ছাপ প্রকট। মাথার ডান দিকটা তীব্র আঘাতে চুরমার হয়ে গেছে প্রায়। যা দিয়ে আঘাত, সেটা পড়ে আছে মাথার পাশে। পাথর, প্রমাণ সাইজ়ের। ওজন? তা কুড়ি কেজি তো হবেই।
গোয়েন্দারা যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছে ছবি তুলছেন নিহতের, ওসি হোমিসাইড যখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন দ্রুত ফরেনসিক পরীক্ষার আয়োজনে, কন্ট্রোল রুম মারফত ওয়ারলেস বার্তা এল, ‘সাসপেকটেড মার্ডার ইন মুচিপাড়া পিএস এরিয়া… নিয়ার শিয়ালদা স্টেশন সাবওয়ে… ভিকটিম আ টিনএজার ..।’
গোয়েন্দাপ্রধান কিংবা নগরপাল স্বয়ং, সকাল-সকাল জোড়া খুনের খবরে বিচলিত হননি কেউই। গড়পড়তা পুলিশি রোজনামচার মাঝে হয় কখনও কখনও এমন। আসে, এমন এক-একটা দিন আসে, কোনও এক অদৃশ্য ষড়যন্ত্রীর অঙ্গুলিহেলনে যাবতীয় খারাপ যেন একসঙ্গে ঘটতে থাকে।
বিচলিত হওয়ার কারণ ঘটল ওসি মুচিপাড়ার বার্তায়, ‘স্যার.. বাচ্চা ছেলে … বয়স এই চোদ্দো-পনেরো হবে .. আইডেন্টিটি এস্ট্যাব্লিশড হয়নি এখনও… যেটুক পাচ্ছি, স্টেশনের ফুটপাথে থাকত .. ভিক্ষে করত … হেড ইনজুরি মাথার বাঁ দিকে.. একটা বড় পাথর দিয়ে মাথায় মারা হয়েছে .. পাথরটায় ব্লাড স্টেইনস আছে…।’
মানে? আবার পাথর? দুটো খুনই পাথর দিয়ে মাথায় মেরে? দুটোই ফুটপাথে? আলেয়া বিবির খুনের মোডাস অপারেন্ডির সঙ্গে হুবহু মিল? তা হলে কি ..? কী-কেন তো পরে, ঘটনার ঘনঘটায় গোয়েন্দারা দিব্যি বুঝতে পারছিলেন নির্যাস— ‘নিশ্চিন্ত আর থাকা গেল না রে তোপসে!’
আধঘণ্টার মধ্যে ফের বার্তাবাহকের ভূমিকায় কন্ট্রোল রুম, ‘সিপি ডিজ়ায়ার্স টু মিট ডিসি ডিডি অ্যান্ড অফিসার্স অফ দ্য হোমিসাইড স্কোয়াড অ্যাট টেন ইন দ্য লালবাজার কনফারেন্স রুম। ডিসি সেন্ট্রাল শ্যাল অলসো রিমেইন প্রেজ়েন্ট উইথ দ্য ওসি-জ় অফ তালতলা, মুচিপাড়া অ্যান্ড হেয়ার স্ট্রিট পুলিশ স্টেশনস।’
.
ঘণ্টাখানেকের বৈঠকে তিনটে খুন নিয়েই কাটাছেঁড়া করলেন নগরপাল। অফিসারদের প্রত্যেকের মতামত জানতে চাইলেন। শুনলেন ধৈর্য ধরে। অল্পসময়ের ব্যবধানে একই ধাঁচের অপরাধের পুনরাবৃত্তি হলে যা আশু জরুরি হয়ে ওঠে, আলোচনা হল তা নিয়েই।
এক, ‘ডিটেকশন’। ঘটে যাওয়া খুনগুলোর কিনারা করা যত দ্রুত সম্ভব। দুই, ‘প্রিভেনশন’। যতক্ষণ না সমাধানসূত্র পাওয়া যাচ্ছে, একই ধরনের খুন আর ঘটতে না দেওয়া।
সিপি এবং ডিসি ডিডি তো বটেই, অন্য অফিসাররাও টের পাচ্ছিলেন, আলোচনা করা এক, আর তার সফল প্রয়োগ আরেক। ‘ডিটেকশন’-এর দিক থেকে ভাবলে, আলেয়া বিবির খুনে আপ্রাণ চেষ্টা করেও সামান্যতম ‘লিড’ও অধরা এখনও। তার মধ্যেই এই জোড়া খুন।
নিহত তিন। একজন মহিলা, পুরুষ একজন, তৃতীয়জন নেহাতই কিশোর। মহিলার পরিচয় জানা গেছে। বাকি দু’জনের এখনও নয়। হয়তো জানা যাবে কয়েকদিনের মধ্যে। কিন্তু পরিচয় সে যা-ই হোক, তিনটে খুনেই কমন ফ্যাক্টরগুলো তীব্র অস্বস্তি উৎপন্ন করছে। খুনির হাতিয়ার তিনটে ক্ষেত্রেই পাথর। তিনটে ঘটনারই সময়কাল শেষ রাত থেকে ভোরের মধ্যবর্তী। এবং ‘ভিক্টিম প্রোফাইল’ তিনটে ক্ষেত্রেই সমগোত্রীয়। আততায়ী বেছে নিয়েছে নিরাশ্রয় ফুটপাথবাসী কাউকে। যাদের খুন করে অর্থাগমের সম্ভাবনা নেই কোনও।
পদ্ধতি এক। টার্গেট-চরিত্র এক। আঘাত হানার সময়টাও এক। ‘ক্রাইম প্যাটার্ন’-এ এত যখন মিল, আততায়ীও এক? যদি আশঙ্কাই সত্যি হয়, যদি একই লোক হয়, তা হলেও নাগাল পাওয়ার মতো সূত্র কই? পার্ক স্ট্রিট মেট্রোর কাছে খুন হওয়া মাঝবয়সি এবং শিয়ালদায় নিহত কিশোরের পরিচয় জানতে পারলে দিশা মিলবে কিছু? যোগসূত্র কোনও?
এ তো গেল ‘ডিটেকশন’-এর সাতসতেরো। কিন্তু ‘প্রিভেনশন’? কী করে হবে ‘প্রিভেনশন’? অত সোজা? এ শহরের পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণ, হাজার হাজার মানুষ ফুটপাথে রাত্রিযাপন করেন এখানে-ওখানে-সেখানে। সম্ভব পাহারা দেওয়া?
সংকট যখন চোখ রাঙায়, সম্ভব-অসম্ভব নিয়ে মাথা ঘামানোর অত সময় থাকে না। অগ্রাধিকার পায় যে ভাবেই হোক মুশকিল আসানের রাস্তা খোঁজা। সিদ্ধান্ত হল, নৈশ নজরদারি বাড়ানো হবে শহরে। তিনটে খুনই হয়েছে সেন্ট্রাল ডিভিশনে, মধ্য কলকাতায়। ঠিক হল, মধ্য কলকাতার সব ওসি নিয়ম করে থাকবেন রাতপাহারায়, চলবে টহলদারি। শুধু গাড়িতে নয়, পায়ে হেঁটেও চালু হবে নৈশ-নজরদারি। শহরের বাকি এলাকার ডিসি-ওসি-দেরও শোনানো হল সতর্কবার্তা, বলা হল রাতের শহরে পুলিশি উপস্থিতি বাড়াতে।
মিটিংয়ের শেষে গোয়েন্দাপ্রধান অর্থাৎ ডিসি ডিডি-কে ঘরে ডেকে নিলেন নগরপাল। কথাচালাচালি হল খানিক।
—কী বুঝছ… খোলাখুলি বলো…
ডিসি ডিডি কয়েক সেকেন্ড ভাবার পর উত্তর দিলেন।
—লুকস কোয়াইট স্ট্রেঞ্জ স্যার … কোনও কানেক্ট এখনও পাওয়া যাচ্ছে না.. অথচ তিনটে খুনই একই ভাবে … সিমিলারিটিটা …
মাঝপথে থামিয়ে দেন নগরপাল।
—সেজন্যই তো বললাম খোলাখুলি বলতে। কী মনে হচ্ছে… সিরিয়াল কিলিং?
উত্তর দেন না গোয়েন্দাপ্রধান। স্রেফ তাকান সিপি-র দিকে। নগরপালও নিরুত্তরই থাকেন।
আশঙ্কা আর উদ্বেগ কবেই বা আর শব্দের তোয়াক্কা করেছে?
.
আশঙ্কা সত্যি হল আপাদমস্তক, উদ্বেগ ঊর্ধ্বগামী হল মাসখানেকের মধ্যেই। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খুনে নিহতদের পরিচয় মেলেনি তখনও, অফিসারদের জানকবুল চেষ্টা সত্ত্বেও। চলছে নৈশপ্রহরা পরিকল্পনামাফিক। তবু ২৭ অগস্ট ফের খুন, ফের ফুটপাথ, ফের পাথর! শিয়ালদা ফ্লাইওভার থেকে নেমে সাবওয়ের পথে এবার, টার্গেট এবারও রাস্তায় ঘুমন্ত, হা-ক্লান্ত, আশ্রয়হীন। মধ্যতিরিশের ভবঘুরে ভিক্ষুক। হননকাল, ভোর চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে।
যে সময়ের কথা, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার দাপট তখনও মাথাচাড়া দেয়নি। একচেটিয়া আধিপত্য ছাপার অক্ষরের। লেখালেখি হচ্ছিল বটে তিনটে একই ধাঁচের খুন নিয়ে, কিন্তু উদ্বাহু হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার উপকরণ ছিল না পর্যাপ্ত। যে সমস্যা রইল না একই কায়দায় চতুর্থ খুনের পর। খবরের কাগজ যা যা ছিল শহরে, একযোগে মাঠে নামল। শিরোনামে চলে এল পুলিশি ব্যর্থতা, ফ্রন্ট পেজ দখল করল রাতের শহরের রহস্যময় ঘাতক। একটি জনপ্রিয় ইংরেজি দৈনিকের সাংবাদিক লিখলেন, ‘Stoneman Strikes Again!’
সেই প্রথম ব্যবহৃত হল ‘স্টোনম্যান’ শব্দটা। যা সমার্থক হয়ে গেল মামলার সঙ্গে, এবং তার চেয়েও ঢের জরুরি, আতঙ্কের আহ্বায়ক হিসাবে দেখা দিল শহর কলকাতার মননে-মানসে।
লালবাজারে বৈঠক হল ফের। কিন্তু প্রয়োজন হল না মিটিং-শেষে কর্তাদের একান্ত আলাপচারিতার। সত্যিটা তখন পরীক্ষা শুরুর ঘণ্টার মতো বাজতে শুরু করেছে কলকাতা পুলিশের ‘ভিতর-বাহিরে অন্তরে অন্তরে’।
সিরিয়াল কিলিং! সিরিয়াল কিলার!
.
স্ট্র্যাটেজি তৈরি হল নতুন করে। ‘নতুন’ বলতে ‘প্রিভেনশন মেকানিজ়ম’-কে ঢেলে সাজানো। হাজার চেষ্টাতেও যখন ‘ডিটেকশন’ এখনও দূর অস্ত, উপায় কি আর? নৈশ প্রহরার জাল আরও বিস্তৃত করা ছাড়া আর কী-ই বা এই পরিস্থিতিতে করণীয়?
‘করণীয়’-র তালিকার সংক্ষিপ্তসার?
এক, শহরের বিভিন্ন থানার অফিসারদের এবং ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট-এর গোয়েন্দাদের যার যেখানে যা সোর্স আছে, সবাইকে পত্রপাঠ মাঠে নামতে হবে। ‘ডিটেকশন’-এর জন্য শহরজুড়ে সোর্স লাগানো হয়েছিল আগেই, লাভ হয়নি। এবার কাজে লাগাতে হবে, ‘প্রিভেনশন’-এর জন্যও। সোর্সদের উপর নির্দেশ থাকবে রাত দশটা থেকে ভোর ছ’টা অবধি রাতপাহারার। এলাকা ভাগ করে দেওয়া হবে প্রত্যেককে। হাতে দিয়ে দেওয়া হবে নির্দিষ্ট এলাকার ম্যাপ। ‘নির্দিষ্ট এলাকার ম্যাপ’ মানে শহরের যে যে জায়গায় ফুটপাথবাসীদের সম্মিলিত রাত্রিবাস, সেই জায়গাগুলোর হাতে আঁকা ভূগোল। রাস্তায় কাউকে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে সোর্স খবর দেবে পুলিশকে। নজরদারিতে সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাবে মধ্য কলকাতা, যা এখনও পর্যন্ত স্টোনম্যানের বিচরণভূমি।
দুই, সোর্স তো নজরদারির সহায়ক-শক্তি মাত্র, আসল কাজটা তো পুলিশকেই করতে হবে। কী ভাবে? ত্রিমুখী রাতপাহারা, সিদ্ধান্ত নিল লালবাজার। গাড়িতে, পায়ে হেঁটে এবং সাইকেলে। শহরের সমস্ত ওসি এবং এসিপি-দের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হল এলাকা। তৈরি হল এলাকাভিত্তিক ‘পেট্রোলিং চার্ট’। ফোকাস, ফুটপাথ। কিন্তু কোন ফুটপাথ? ফুটপাথ তো অসংখ্য। ‘যত মত তত পথ’, আর ‘যত পথ তত ফুটপাথ’, শহরের এ-মাথা থেকে ও-মাথা। স্টেশন চত্বর, বাস টার্মিনাস, হাসপাতালের বাইরের রাস্তা, এমন কিছু জায়গায় তবু একত্রে রাত্রিবাস করেন ফুটপাথবাসীরা। কিন্তু তার বাইরেও পড়ে থাকে হাজার হাজার অলিগলি, পড়ে থাকে অগুনতি আনাচকানাচ। সর্বত্র সম্ভব নজরদারি? অসম্ভবকে যতটা সম্ভব করা যায়, ঝাঁপাল কলকাতা পুলিশ। হেঁটে, গাড়িতে, সাইকেলে।
তিন, জিআরপি-র ( গভর্নমেন্ট রেলওয়ে পুলিশ) সঙ্গে সমন্বয়ে হাওড়া-শিয়ালদা স্টেশনের বাইরে-ভিতরে নৈশপ্রহরায় সামান্যতম ঢিলে দেওয়া যাবে না। বিশেষ করে শিয়ালদায়। এমন হতেই পারে, ঘাতক আসছে শহরের বাইরে থেকে রেলপথে। কাজ হাসিল করে চম্পট দিচ্ছে রেলপথেই, ভোরের ট্রেনে। কাকভোরের ট্রেনগুলোর যাত্রীদের উপর নজরদারির তীব্রতা থাকতে হবে বিরামহীন।
চার, নজরদারির উপর নজরদারি। প্ল্যানমাফিক প্রহরা চলছে কিনা, তার সরেজমিন তদারকির দায়িত্বে প্রতি রাতে রাস্তায় থাকবেন একজন ডিসি পদমর্যাদার অফিসার। এবং নৈশ অভিযানের খুঁটিনাটি সমন্বয়ের ভার সামলাবেন আরেকজন ডিসি, লালবাজারের কন্ট্রোল রুম থেকে।
কিন্তু এত করেও শেষরক্ষা আর হল কই? মুচিপাড়া এলাকায় চতুর্থ খুনটা হয়েছিল ২৭ অগস্ট। তার ঠিক দশদিনের মাথায়, ৬ সেপ্টেম্বর, ফের লালবাজারের রক্তচাপ বাড়িয়ে দিল স্টোনম্যান। হাওড়া ব্রিজে ওঠার মুখে উত্তরদিকের ফুটপাথে অজ্ঞাতপরিচয় বছর পঁয়ত্রিশের যুবক খুন। চেহারা ভবঘুরে প্রকৃতির, মাথায় বাঁ দিকটা থেঁতলানো প্রায় কুড়ি কেজি ওজনের পাথরের আঘাতে। যে পাথরটা, অন্য খুনগুলোর মতোই, পড়ে মৃতদেহের পাশে। দেহ আবিষ্কৃত হল ভোরের দিকে। ময়নাতদন্ত জানাল, হত্যার সময় রাত তিনটে থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে।
পঞ্চম খুনের ধাক্কা সামলাতে না সামলাতেই খুন নম্বর ছয় আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে। ৮ সেপ্টেম্বর। ঘটনাস্থল এবার ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিটে, লালবাজার থেকে বড়জোর সাত-আটশো মিটার দূরত্বে। নিহত দৃশ্যতই ভিক্ষে করে জীবিকানির্বাহ করতেন। বয়স তিরিশের কোঠায়। পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজনই, তবু লিপিবদ্ধ থাক তথ্যের স্বার্থে, খুন একই কায়দায়, খুনির হাতিয়ারও একই। পাথর।
শহর জুড়ে ততদিনে ত্রাসের নাম স্টোনম্যান। আতঙ্কের ঠিকানা ফুটপাথ। খবরের কাগজ না হয় ছেড়েই দিলাম, পথেঘাটে-বাসে-ট্রামে-পাড়ার রকের সান্ধ্য আড্ডায় চর্চার বিষয় একটাই। স্টোনম্যান। কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে আমবাঙালির কথাচালাচালি।যাতে উদ্বেগ যত না,স্বীকার করা ভাল, তার চেয়েও বেশি ধরা পড়ছে রহস্যযাপন, ধরা পড়ছে কিছুটা ‘চাচা আপন প্রাণ বাঁচা’ মার্কা মধ্যবিত্ত স্বস্তিও।
—মারছে তো ফুটপাথে শুয়ে থাকা লোককে। মোদ্দা কথা, মাথার উপর ছাদ আছে যাদের, তারা সেফ। তোর-আমার রিস্ক নেই।
—সেলফিশ মিডলক্লাস মাইন্ডসেট একেই বলে! ফুটপাথের লোকগুলো মানুষ নয়? ওদের জীবনের দাম নেই কোনও?
—তা তো বলিনি। স্টোনম্যানের টার্গেট গ্ৰুপ যে ফুটপাথে রাত কাটানো লোকজন, এতে তো কোনও ডাউট নেই আর। আমি শুধু ভাবছি, একটা লোক খুনের পর খুন করে যাবে এভাবে, আর পুলিশ আঙুল চুষবে, অপেক্ষা করবে পরের খুনটার জন্য?
—কাগজে তো পড়লাম স্পেশ্যাল নাইট পেট্রোলিং শুরু হয়েছে…
—তাতে লাভ তো কিছু হচ্ছে না! খুন তো করেই যাচ্ছে ইচ্ছেমতো। টিকিটাও ছোঁয়া যাচ্ছে না খুনির। লালবাজারের সঙ্গে নাকি স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের তুলনা করা হয়। এই তো নমুনা!
—তা যা বলেছিস! এদের একজন ফেলুদা বা ব্যোমকেশ দরকার, বুঝলি? না হলে কিস্যু হওয়ার নয়।
ছিছিক্কার চলছিল খবরের কাগজেও দিনের পর দিন। ‘ছ’টি খুনের পরও অন্ধকারে পুলিশ’, ‘লালবাজারের জবাবদিহি চাইল মহাকরণ’, ‘স্টোনম্যানকে ধরতে ল্যাজেগোবরে কলকাতা পুলিশ’… এই জাতীয় হেডিংসংবলিত খবর তখন নিত্যনৈমিত্তিক।
পড়তে-শুনতে খারাপ লাগলেও স্বীকার্য, সমালোচনা প্রাপ্যই ছিল। একটা লোক একই কায়দায় রাতের শহরে খুন করে যাচ্ছে একের পর এক, আর কিস্যু করতে পারছে না কলকাতা পুলিশ, জটিল থেকে জটিলতর মামলার সফল কিনারার জন্য যাদের দেশজোড়া নাম, ‘স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড’ অভিধাপ্রাপ্তি?
অথচ চেষ্টায় তিলমাত্র খামতি ছিল না লালবাজারের। রাতের শহরে একাকী পথচারী দেখলেই পথ আটকে জেরা করছিল পুলিশ। উত্তরে সামান্যতম অসংগতি পেলেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল লালবাজারে, চলছিল জিজ্ঞাসাবাদ ঘণ্টার পর ঘণ্টা। জনাপঞ্চাশ ভবঘুরে প্রকৃতির লোককে আটক করেও তবু সূত্র থাকছিল নাগালের বাইরে। তদন্ত যে তিমিরে ছিল, সেই তিমিরেই আটকে থাকছিল স্থাণুবৎ। পুলিশে ক্রমশ ভরসা হারাচ্ছিল রাতের কলকাতা।
এবং ভরসাহীনতার মরিয়া প্রতিফলন ঘটছিল, দিন যাচ্ছিল যত। পুলিশ যখন পারছে না, নিজেদের সুরক্ষা-বলয় ফুটপাথবাসীরা নিজেরাই তৈরি করে নিচ্ছিলেন যথাসাধ্য। পালা করে চলছিল রাত জাগা। একদল ঘুমোচ্ছিলেন রাত দশটা থেকে দুটো। তখন বাকিরা তাস খেলছিলেন। দুটো থেকে অন্যদের জাগার পালা, বাকিদের ঘুমের। ভবঘুরে জাতীয় কাউকে দেখলেই রে রে করে তেড়ে যাচ্ছিলেন ওঁরা। চলছিল দেদার চড়থাপ্পড়, ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে রেখে প্রশ্নবাণ এবং কিলঘুসি।
—বল, এত রাতে এখানে কেন?
—বলবে আবার কী, নির্ঘাত এই শালাই স্টোনম্যান! মার ব্যাটাকে!
—হ্যাঁ, মেরে তক্তা করে দি চল…
—কিন্তু পাথরটা কোথায়? বল বল… পাথরটা কোথায় রেখেছিস? না বললে তোর মাথাতেই আজ পাথর ভাঙব।
কত পথচারীকে যে সে-সময় গণপিটুনির হাত থেকে উদ্ধার করেছে পুলিশ, হিসেব নেই। মেরে মুখচোখ ফাটিয়ে দিয়েছে উন্মত্ত জনতা, ‘বিশ্বাস করুন, আমি স্টোনম্যান নই’-এর আকুল আর্তি উপেক্ষা করেই। খবর পেয়ে পুলিশি হস্তক্ষেপে প্রাণে বেঁচেছেন একাধিক নিরপরাধ মানুষ। আর ক্ষোভে-বিদ্রুপে-সমালোচনায় জেরবার পুলিশ ভেবেছে প্রতিটি মুহূর্তে, এর শেষ কোথায়? কী আছে শেষে?
‘শেষ কোথায়’-এর ভাবনার মাঝেই সপ্তম ঘটনা। অকুস্থল, ফের মুচিপাড়া থানা এলাকা। এবার বৈঠকখানা রোড। শিকার এবার তেগা রাই নামের এক অনূর্ধ্ব তিরিশ যুবক। বাড়ি বাড়ি দুধ সরবরাহ করার কাজ করতেন। রাত কাটাতেন ফুটপাথে। রক্তাক্ত অবস্থায় অচৈতন্য পড়ে থাকা তেগাকে যখন পাওয়া গেল রাত তিনটে-সোয়া তিনটে নাগাদ, তখনও প্রাণ আছে দেহে। পাথরের আঘাতে মাথার বাঁ দিক ভেসে যাচ্ছে রক্তে। চুঁইয়ে পড়ে লাল হয়ে গেছে ফতুয়া। তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হল মেডিক্যাল কলেজে। জ্ঞান তো হারিয়েইছিলেন, প্রাণ হারাতে লাগল আটচল্লিশ ঘণ্টা। সাত নম্বর খুন।
প্রথমটা ৪ জুন। জোড়া খুন ১৯ জুলাই। তারপর ২৭ অগস্ট, ৬ সেপ্টেম্বর, ৮ সেপ্টেম্বর, ১১ সেপ্টেম্বর। একশো দিনের মধ্যে একই ‘মোডাস অপারেন্ডি’-তে সাত-সাতটা খুন। হয়নি, কখনও এমনটা হয়নি কলকাতা পুলিশের ইতিহাসে। এতগুলো খুনের পরও ‘লিড’ পেতে ব্যর্থ হয়েছে লালবাজার, এমনটা ঘটেনি কখনও। প্রশ্ন উঠল বিধানসভায়, লোকসভাতেও আলোচিত হল কলকাতা পুলিশের ব্যর্থতা। দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশের সংবাদমাধ্যমেও জায়গা করে নিল স্টোনম্যান। বিলেতের ‘দ্য গার্ডিয়ান’ পত্রিকাতে সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ প্রকাশিত হল কলকাতার মধ্যরাতের সিরিয়াল-কিলারকে নিয়ে।
.
সিরিয়াল-কিলিং। ঠিক কী উপাদানে তৈরি হয় একজন সিরিয়াল-কিলারের অন্তরমহল, সে নিয়ে বিশ্বজুড়ে বিবিধ গবেষণা হয়ে আসছে বহুকাল ধরে। কোন ব্যক্তিবিশেষের সিরিয়াল-কিলার হয়ে ওঠার নেপথ্যে কয়েকটি কারণকে সচরাচর নির্দিষ্ট করে থাকেন অপরাধ-বিজ্ঞানীরা।
এক, সম-অনুভূতির অভাব। সহানুভূতির অভাব নয়, অভাব সম-অনুভূতির, পরিভাষায় যাকে আমরা বলি ‘empathy’। মনোজগতে ‘empathy’-র অস্বাভাবিক রকমের অভাব একটা পর্যায়ের পর একজন মানুষকে ‘psychopath’ বা মনোবিকারগ্রস্ত করে তোলে। যে বিকারের বহিঃপ্রকাশ ঘটে কার্যকারণহীন নির্বিচার হত্যায়।
দুই, নিজের প্রতি বহির্বিশ্বের কৌতূহল উৎপন্ন করার উদগ্র বাসনা, পরিভাষায় ‘attention-seeking’।এবং নিজেকে যেনতেনপ্রকারেণ ক্ষমতাবান এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করার মরিয়া প্রবণতা। পরিণতি, জন্ম নেয় বিকার। যে বিকারের উৎস সিংহভাগ ক্ষেত্রে নিহিত থাকে সমস্যাক্লিষ্ট শৈশবে-কৈশোরে। গবেষণালব্ধ তথ্য বলছে, সিরিয়াল কিলারদের অনেকেই নানান যন্ত্রণার শিকার হয়েছে ছোটবেলায়। সে মানসিক হোক বা শারীরিক। কেউ হয়তো ছোট থেকেই সাক্ষী থেকেছে মা-বাবার অশান্ত দাম্পত্যের, সাক্ষী থেকেছে বিচ্ছেদের। কেউ হয়তো প্রাপ্য স্নেহ-ভালবাসাটুকু পায়নি অভিভাবকদের কাছে। কেউ হয়তো আবার শিকার হয়েছে পরিচিত কারও যৌন নির্যাতনের।
তিন, স্রেফ উত্তেজনা আহরণের জন্য খুন। বিজাতীয় আনন্দের জন্য খুন। অন্যকে যন্ত্রণাক্লিষ্ট করার জন্য খুন। লক্ষ্য যেখানে অন্য কিছু নয়, ‘থ্রিল’। সম্পূর্ণ অপরিচিত এবং নিরপরাধ কাউকে যন্ত্রণা দিয়ে শিরা-উপশিরায় বাড়তি অ্যাড্রিনালিনের আমদানি।
আধুনিক সভ্যতার ইতিহাসে ‘সিরিয়াল কিলার’ বলতেই প্রথম যে নামটা উঠে আসে অবধারিত, ‘জ্যাক দ্য রিপার’! যিনি ১৮৮৮ সালে লন্ডনে অন্তত পাঁচজন দেহপসারিণীকে খুন করে শিরোনামে চলে এসেছিলেন রাতারাতি। হইচই পড়ে গিয়েছিল বিশ্বজুড়ে।
নাম আরও করা যায়। যেমন উনিশ শতকের শেষ দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পরপর ন’টা খুন করা H. H. Holmes কিংবা মোটামুটি সমসময়েই ফ্রান্সে ১১ জন মহিলা এবং শিশুকে উপর্যুপরি খুনের নেপথ্যে থাকা সিরিয়াল-ঘাতক Joseph Vacher, যিনি কুখ্যাত হয়েছিলেন ‘The French Ripper’ নামে।
এ তো গেল বিদেশের কথা। ভারতে? রমন রাঘবের কথা উল্লেখ না করলে অসম্পূর্ণ থেকে
যাবে এই লেখা। ১৯৬৬ থেকে ৬৮–র মধ্যে মুম্বই শহরতলি এবং পুনেতে দু’দফায় অন্তত পঁয়ত্রিশটা খুনের পর গ্রেফতার হয়েছিল এই রমন রাঘব। প্রতিটি খুনেই শিকার ছিল হয় ফুটপাথবাসী, নয় বস্তিতে বসবাসকারী দরিদ্রতম শ্রেণিভুক্ত কেউ। চূড়ান্ত আতঙ্ক গ্রাস করেছিল বাণিজ্যনগরীকে। ধরা পড়ার পর মনোবিদরা রমনের সঙ্গে বহু সময় কাটিয়েছিলেন। জানিয়েছিলেন, সে সংশোধনের অযোগ্য মনোবিকারগ্রস্ত। মানসিক অসুস্থতার কথা ভেবেই নিম্ন আদালতের ফাঁসির রায় উচ্চতর কোর্টে বদলে গিয়েছিল যাবজ্জীবন কারাবাসে।
সিরিয়াল-কিলারের আতঙ্ক ফের মুম্বইয়েই ফিরে এসেছিল আটের দশকের মাঝামাঝি। ১৯৮৩ থেকে ’৮৬-র মধ্যে বারোটা খুন হয়েছিল একই কায়দায়। ফুটপাথবাসীদের মাথায় পাথর মেরে। ধরা যায়নি সেই ‘স্টোনম্যান’-কেও। এক ডজন খুনের পর আচমকাই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল নিধননাট্য। বারো নম্বরই শেষ।
তা হলে কি সেই ‘স্টোনম্যান’-ই আবির্ভূত ফের কলকাতায়? গোয়েন্দা বিভাগের টিম পাড়ি দিল মুম্বইয়ে, তখনকার খুনগুলোর বিষয়ে আলোচনা করতে। এবং এতসবের মধ্যেই সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ‘হঠাৎ আলোর ঝলকানি’ দেখতে পেল লালবাজার। রাতের শহরের টহলদারি টিমগুলোর একটা শিয়ালদা স্টেশনের কাছ থেকে আটক করল এক সন্দেহভাজনকে।
সন্দেহভাজন তো প্রায় প্রতিদিনই কেউ না কেউ আটক হচ্ছিল। এক্ষেত্রে উৎসাহিত হওয়ার কারণ? ভবঘুরে প্রকৃতির লোকটির বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। ঘুরছিলেন বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রিটের পাশে ইতস্তত। পুলিশ আটকেছিল।
—নাম কী আপনার?
—দুনিয়া মালিক।
—মানে?
—দুনিয়া মালিক। মানে দুনিয়ার মালিক।
—ইয়ার্কি মারার জায়গা পাননি? আসল নামটা বলুন।
—নামের আবার আসল-নকল? মা-বাবা নাম রেখেছিল মহম্মদ এক্রাম। কিন্তু ওটা নকল নাম। আসল নাম দুনিয়া মালিক।
—বেশ তো দুনিয়া মালিক, বাড়ি কোথায়? এত রাতে এখানে কেন?
—পুরো দুনিয়াটাই তো আমার বাড়ি। নিজের বাড়িতে ঘুরতে পারব না সাব?
অফিসাররা মুখ চাওয়াচাওয়ি করেন। ব্যাটা হয় মাথায়-ছিট আধপাগলা, নয় সাতসেয়ানার ক্যাপ্টেন। আন্দাজে ঢিল ছোড়েন এক সাব-ইনস্পেকটর।
—বেশ, বুঝলাম। রাতে থাকেন কোথায়? ঘুমোন কোথায়?
—ঘুমোই না স্যার, ফুটপাথে ফুটপাথে ঘুরি স্যার। দুনিয়ার মালিকের দুনিয়ায় কত লোকের মাথার ওপর ছাদ নেই, রাতে ঘুরে ঘুরে দেখি।
—ঘুরে ঘুরে দেখেন আর পাথর দিয়ে খুন করে বেড়ান, তাই তো?
ভাবলেশহীন উত্তর আসে।
—আমি দুনিয়ার মালিক। কেন খুন করতে যাব স্যার? তবে ফুটপাথে এইভাবে যারা রাত কাটায়, সেটা কোনও বাঁচা হল স্যার? ইয়ে ভি কোই জিন্দেগি হ্যায়?
—গাড়িতে উঠুন।
ভোররাত থেকে লালবাজারে শুরু হল ‘দুনিয়া মালিক’-কে ম্যারাথন জেরা। কথাবার্তা কখনও এলোমেলো, অসংগতিপূর্ণ, কখনও সামান্য হলেও স্বাভাবিক। জানা গেল, বিহারের সীতামারি জেলার বাসিন্দা এই মহম্মদ এক্রাম। কলকাতায় এসেছিলেন বাবার সঙ্গে বছর কুড়ি-পঁচিশ আগে। বাবা মহম্মদ ঈশা দিনমজুরের কাজ করতেন এদিক-ওদিক। বাবা মারা যাওয়ার পর ভবঘুরে জীবনযাপন। এই লোক স্টোনম্যান?
জেরাপর্ব শেষে নগরপাল বৈঠক সারেন গোয়েন্দাপ্রধানের সঙ্গে।
—তোমার ‘গাট ফিলিং’ কী বলছে?
নগরপালের প্রশ্নের জবাবে গোয়েন্দাপ্রধানকে দ্বিধাগ্রস্ত শোনায়।
—কনফেস তো করেনি এখনও। তবে ‘ক্লিন চিট’ দেওয়ার মতো জায়গাতেও নেই আমরা। আরও ডিটেইলড ইন্টারোগেশন দরকার স্যার……
—সে তো দরকারই। মেন্টালি আনস্টেবল একটু, বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু সিরিয়াল কিলারদের ‘মেন্টাল ইনস্টেবিলিটি’ থাকেই নানা ধরনের। এই যে ‘দুনিয়া মালিক’ বলছে, একটা ‘ইমাজিনড সেন্স অফ পাওয়ার’ থেকে বলছে।
—আর সেই ‘পাওয়ার’ বা ক্ষমতা ফলানোর বোধ থেকেই এভাবে পরের পর খুন….
—অসম্ভব নয়… একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।
—কিন্তু স্যার… লোকটার চেহারাটা খেয়াল করেছেন?
—হ্যাঁ, আই ওয়াজ় কামিং টু দ্যাট… ওই ল্যাকপেকে চেহারায় পনেরো-কুড়ি কেজি ওজনের পাথর তুলে আছড়ে মারবে… এটা ঠিক…
—কিন্তু এমনও তো হতে পারে, আমরা স্টোনম্যান-স্টোনম্যান ভাবছি, আসলে এটা একটা গ্যাং। স্টোনম্যান নয়, ‘স্টোনমেন’। একাধিক লোক মিলে প্ল্যান করে কাজটা করছে।
—আমার যদিও মনে হচ্ছে একজনই, তবে তুমি যা বলছ, নট এন্টায়ারলি ইমপসিবল। যা অবস্থা এখন, সব অপশনই মাথায় রেখে এগোতে হবে। যেখানে যেখানে খুনগুলো হয়েছে, তার কাছাকাছি তো কোনও পাথরের স্তূপ ছিল না। যে মেরেছে, পাথরটা সঙ্গে নিয়ে এসেছে। বা আগে থেকে কাছেপিঠে এনে রেখেছে।
—ফুটপাথ বলে আরও সমস্যা হচ্ছে স্যার। ধুলোবালি আর ‘একস্টারন্যাল এলিমেন্টস’-এ একটা কেসেও কোনও ডেভেলপ করার মতো ফুটপ্রিন্টসও পাওয়া যায়নি। পেলে অন্তত এই ‘দুনিয়া মালিকের’ সঙ্গে মেলানো যেত। কোথাও কোনও চিহ্ন রেখে যাচ্ছে না লোকটা।
—যা নেই, তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। আপাতত এই মহম্মদ এক্রামের একটা ‘সাইকোলজিক্যাল এগজ়ামিনেশন’ দরকার। মনস্তত্ত্ববিদদের পরামর্শ নেওয়াটাই জরুরি হয়ে পড়ছে।
—রাইট স্যার। কালই ব্যবস্থা করছি। কিন্তু তাতেও কি ডেড শিয়োর হওয়া যাবে… আই মিন… যতক্ষণ না নিজে কনফেস করছে…
—দেখাই যাক… আর মনে রেখো, ইংরেজিতে একটা কথা আছে, ‘The proof of the pudding is in the eating’… ডেডশিয়োর হওয়ার ওটাই উপায়। এই ‘দুনিয়া মালিক’-ই যদি স্টোনম্যান হয়, তা হলে সাত নম্বর খুনটাই লাস্ট খুন। আর হবে না। যদি হয়, বুঝতে হবে, এক্রামকে মিথ্যে সন্দেহ করছি আমরা।
—স্যার…
নগরপালের ঘর থেকে বেরনোর পর গোয়েন্দাপ্রধানের কানে বাজতে থাকে কথাগুলো। এ-ই যদি স্টোনম্যান হয়, তা হলে শেষ খুনটাই ‘শেষ’। না হলে বুঝতে হবে…
না হলে যা বুঝতে হবে, সেটাই বোঝা গেল অক্টোবরের ১৯ তারিখ। সপ্তম খুনের এক মাস আট দিন পরে যখন গোয়েন্দাপ্রধানের কাঁচা ঘুমে ছেদ ঘটাল মধ্যরাতের ফোন।
—ক্রিং ক্রিং!!
—নমস্কার স্যার, আবার!
—মানে?
—আর আহমেদ ডেন্টাল কলেজের কাছে স্যার… সিইএসসির ট্রান্সফর্মার আছে একটা…
—তুমি শিয়োর? আই মিন মোডাস অপারেন্ডি…
—হান্ড্রেড পার্সেন্ট স্যার… যা শুনলাম… জাস্ট দা সেম…
—তা হলে আশঙ্কাই সত্যি হল? গত এক মাসের খচখচানিটাই দেখা দিল রূঢ়তম বাস্তব হয়ে? ‘আবার সে এসেছে ফিরিয়া?’
‘ফিরিয়া যে এসেছে’, মৃতদেহ দেখার পর সন্দেহ ছিল না আর একচিলতেও। উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা-দুশ্চিন্তার ত্র্যহস্পর্শ ফের গ্রাস করল লালবাজারকে। এবার?
তদন্তের বিজ্ঞান বলে, অপরাধীকে ধরতে হলে অপরাধীর মনের মধ্যে ঢোকার চেষ্টা করো। এবং ভাবার চেষ্টা করো অপরাধীর মতো করে। কে স্টোনম্যান? ‘কে’, সেটা পরে হবে। আগে চিন্তা করা দরকার, কী ভাবে?
স্টোনম্যানের ভাবনা কোন খাতে বইছে, সেটা নিয়ে মাথা খাটানো বেশি জরুরি। কীভাবে পুলিশকে, ফুটপাথবাসী রাত-জাগা জনতার চোখে ধুলো দিয়ে নিরীহ মানুষকে মেরে যাচ্ছে লাগাতার? আগে থেকেই জরিপ করে নিচ্ছে, পুলিশ প্রহরা কোথায় কোথায়? তারপর খুঁজে নিচ্ছে নজরদারিহীন নির্জন কোনও ফুটপাথ? এটা বুঝে গেছে, হাজার হাজার ফুটপাথবাসীকে সারারাত পাহারা দেওয়া পুলিশের পক্ষে অসম্ভব? সেই মতো শিকার খুঁজে নিচ্ছে? এবং শিকার চিহ্নিত করার পর সম্ভাব্য শিকারের আশেপাশেই কি শুয়ে থাকছে পাথর নিয়ে? আর রাত গভীর হলে আঘাত হানছে নির্মম নৃশংসতায়?
আক্ষরিক অর্থেই দিশেহারা পুলিশ তখন যেভাবে পারল চেষ্টা করল অপরাধীর মনের হদিশ পাওয়ার। এবং ঘটতে থাকল অদ্ভুতুড়ে কাণ্ড কিছু। স্টোনম্যান মামলার তদন্তের সঙ্গে শুরু থেকে ওতপ্রোত জড়িয়ে ছিলেন, এমন একজন অফিসারের স্মৃতিচারণ তুলে দিলাম।
‘তখন পাগল পাগল লাগছিল নিজেদের। যার যা মনে হচ্ছে করছিলাম। রাতের পর রাত জাগছি, ভোরে ফিরছি। কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে সারাদিন অফিস করে ফের রাতে বেরিয়ে পড়ছি। মাথা কাজ করছিল না বেশিরভাগ সময়। আট নম্বর খুনের পর এক রাতে যখন টহল দিচ্ছি শিয়ালদা স্টেশন এলাকার আশেপাশের ফুটপাথে, হঠাৎ দেখলাম চাদরমুড়ি দিয়ে একজন মুখ বার করে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। তাকানোটা সন্দেহজনক। আরে এ ব্যাটা জেগে আছে কেন? ওভাবে আশেপাশে তাকাচ্ছেই বা কেন?
আমি করলাম কী, সোজা গিয়ে দাঁড়ালাম চাদরমুড়ি দেওয়া লোকটার সামনে। চাদরটা টেনে সরিয়ে দিলাম গা থেকে। টর্চ ফেললাম মুখে। ‘কে রে তুই?’ জিজ্ঞেস করার আগেই থমকে গেলাম চেহারাটা দেখে। আরে! এ তো বহুদিনের চেনা মুখ। ব্যাচমেট। একই সঙ্গে পুলিশ ট্রেনিং কলেজে কাটিয়েছি এক বছর। তারপর কর্মসূত্রে কলকাতা পুলিশে দীর্ঘদিনের সহকর্মী, অভিন্নহৃদয় বন্ধু। এ তো ওসি মুচিপাড়া! এখানে কী করছে?
—কী আর করব বল? আমার এলাকাই তো স্টোনম্যানের বেশি পছন্দ। কী আর করব? শুয়ে আছি ফতুয়া-পায়জামা পরে। যদি ধরতে পারি হাতেনাতে! শুধু আমি নয়, বাঁদিকে চার-পাঁচটা লোকের পরে আমার এক সাব-ইনস্পেকটর শুয়ে আছে।
—এভাবে সারারাত থাকবি?
—উপায় কী আর? চাকরিটা বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করছি আর কী! তবে শুধু আমি নয়। মৌলালিতে যা, দেখবি ওসি এন্টালিও শুয়ে আছে ফুটপাথে।
—অ্যাঁ! সে কী রে!
—আরে ভাই হ্যাঁ! তুইও গিয়ে বি বি গাঙ্গুলি স্ট্রিটের ফুটপাথে অন্যদের সঙ্গে শুয়ে পড়। রাস্তায় ঘুরে তো কিছু হল না, হবেও না আর। তাই স্ট্র্যাটেজি পালটেছি।’
স্ট্র্যাটেজি অবশ্য স্টোনম্যানও পালটে ফেলছিল নিঃশব্দে। চৌঠা জুন থেকে এগারোই সেপ্টেম্বরের মধ্যে সাতটা খুন। গড় ধরলে প্রতি দু’সপ্তাহে একটা। মুচিপাড়ায় অষ্টম খুনটা ঘটেছিল সপ্তমের একমাস আটদিন পরে, যখন পুলিশ সামান্য স্বস্তির অবকাশ পেয়েছে, এবং মনে করছে স্টোনম্যান পর্বের হয়তো ইতি।
নয় নম্বর খুনটা করতেও মাসখানেকের বেশিই সময় নিল স্টোনম্যান। নজরদারি আর রাতপাহারা জারি থাকলেও যখন স্বাভাবিক নিয়মেই শৈথিল্য এসেছে কিছুটা, ঠিক তখন, নভেম্বরের ২৬ তারিখ। ফের শিয়ালদা ফ্লাইওভারের সাবওয়েতে, নীলরতন সরকার হাসপাতাল থেকে ক্রিকেটবল-ছোড়া দূরত্বে। পাথরের আঘাতে ফের এক বছর চল্লিশের অজ্ঞাতপরিচয় ফুটপাথবাসীর ভবলীলা সাঙ্গ।
ফের শুরু তেড়েফুঁড়ে নজরদারি, এবং এবার দু’মাস কোনও সাড়াশব্দ করল না স্টোনম্যান। নিজের উপস্থিতি জানান দিল বছর পার করে, ১৯৯০-এর ২৯ জানুয়ারি, আচমকা। প্রফুল্ল সরকার ষ্ট্রিটে আনন্দবাজার পত্রিকার অফিসের কাছের ফুটপাথে শায়িতা এক মহিলার মাথা চুরমার হয়ে গেল পাথরের আছড়ানিতে। মৃতার বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি, নাম শান্তি মান্না। স্বামী মারা গিয়েছেন বেশ কিছুদিন হল। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, পেশায় যৌনকর্মী। বেশিরভাগ রাত ফুটপাথেই কাটাতেন।
স্টোনম্যানের ধরা পড়ার আশা তখন প্রায় একরকম ছেড়েই দিয়েছে পুলিশ। মিডিয়াও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে পুলিশি ব্যর্থতা নিয়ে নিউজ়প্রিন্ট খরচা করতে করতে। ‘কে স্টোনম্যান?’, ‘কেন স্টোনম্যান?’ এসব প্রশ্নের থেকে তখন ঢের বেশি কৌতূহল পরের খুনটা নিয়ে। এরপর কবে-কখন-কোথায়?
খুন নম্বর এগারোয় চমকে দিল স্টোনম্যান। প্রথম দশটা খুন হয়েছিল মধ্য কলকাতায়। নজরদারি কেন্দ্রীভূত ছিল বউবাজার-মুচিপাড়া-বড়বাজার-পোস্তা-জোড়াসাঁকো-এন্টালি অঞ্চলে। একাদশতম খুনে নিজের অপরাধ-বৃত্ত বিস্তৃত করল স্টোনম্যান। পা রাখল দক্ষিণ কলকাতায়। দশম খুনের ঠিক একুশ দিন পরে। ২০ ফেব্রুয়ারি।
বেকবাগানের মোড়ে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোডের পশ্চিম ফুটপাথে আবিষ্কৃত হল আরেক হতভাগ্যের দেহ। যথারীতি ভারী পাথর দিয়ে মাথাটা থেঁতলানো। নিহতের স্থানীয় নাম ‘মাস্তান’, বয়স বছর চল্লিশের কাছাকাছি। ভিক্ষা করেই দিনযাপন করতেন।
আগের দশটা খুনের সঙ্গে তফাত বলতে, পদচিহ্ন রেখে গেছে স্টোনম্যান। খুনে ব্যবহৃত পাথরটা পড়ে ছিল মৃতদেহ থেকে চার গজ দূরে।একটা ড্রেনের মধ্যে। খুনের পরে আততায়ী স্পষ্টতই পাথরটাকে সরিয়ে নিয়ে যায়। এবং সরানোর সময়ই মৃতের রক্তস্রোতে পা পড়ে। ফুটপ্রিন্টস সংগ্রহ করতে ছুটে এলেন বিশেষজ্ঞরা বাঁ পায়ের ছাপ পাওয়া গেল তিনটে। ডান পায়ের ন’টা। পায়ে জুতো ছিল না। আগের রাতে বৃষ্টি হয়েছিল খানিক। বাঁ পায়ের তিনটে ছাপ পড়েছে অস্পষ্ট, বাকি মিলিয়ে গেছে। ডান পায়ের ছাপগুলো অক্ষত এবং মোটামুটি ‘ডেভেলপযোগ্য’।
বিশেষজ্ঞরা পায়ের ছাপ পরীক্ষা করে দুটো সিদ্ধান্তে এলেন। এক, স্টোনম্যানের চেহারা মাঝারি গড়নের হওয়ারই সম্ভাবনা। খুব লম্বা-চওড়া সম্ভবত নয়। দুই, ঘাতকের ডান পায়ের বুড়ো আঙুল অস্বাভাবিক লম্বা।
কিন্তু এটুকু ‘লিড’ আর কতটাই বা কাজে আসবে? ধরা পড়লে তবেই না পায়ের ছাপ মিলিয়ে নিঃসংশয় হওয়ার প্রশ্ন।
দিগ্ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন গোয়েন্দা বিভাগের পোড়খাওয়া অফিসাররা, অসংখ্য জটিল মামলার সমাধান যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে করে এসেছেন ঈর্ষণীয় পেশাদারি দক্ষতায়। এবং সর্বগ্রাসী হতাশা মনের দখল নিলে একটা পর্যায়ের পর যা স্বাভাবিক, যুক্তি-বুদ্ধিকে লাস্ট বেঞ্চে পাঠিয়ে দিয়ে সামনের সারিতে কেউ কেউ জায়গা দিলেন অন্ধ বিশ্বাসকে।
ওসি হোমিসাইড স্বয়ং ডেকে পাঠালেন এক পরিচিত জ্যোতিষীকে। জানতে চাইলেন, কবে হতে পারে এই যন্ত্রণামুক্তি? কবে ধরা পড়বে স্টোনম্যান? কেমন দেখতে হতে পারে স্টোনম্যান? কেমন হতে পারে চালচলন?
জ্যোতিষী বিস্তর গণনা-টননা করে রায় দিলেন, সুসংবাদ আসন্ন। স্টোনম্যান ধরা পড়বে শীঘ্রই। জানালেন আরও, স্টোনম্যান বকের মতো লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটে। এমন হাঁটার ধরন যাঁদের রাতের শহরে, তাদের চিহ্নিত করতে পারলে রহস্যভেদ নাকি স্রেফ সময়ের অপেক্ষা।
বিচারবুদ্ধিকে বন্ধক রাখলে যা ঘটতে পারে, তার বিবরণী থাকুক এক প্রত্যক্ষদর্শী অফিসারের বয়ানে।
‘নিয়মমাফিক সারারাত টহল দিয়ে ফিরছিলাম লালবাজারে। সঙ্গী এক সাব-ইনস্পেকটর আর দুই কনস্টেবল। গাড়ি যখন আকাশবাণী পেরিয়ে এগোচ্ছে রাজভবনকে ডান হাতে রেখে, হঠাৎ সঙ্গী সাব-ইনস্পেকটরের পরিত্রাহি চিৎকারে হতচকিত হয়ে ব্রেক কষল ড্রাইভার। ‘আরে, থামান থামান। ওই তো!’
‘ওই তো!’ মানে? মানে বোঝার আগেই এক লাফে গাড়ি থেকে নেমে দৌড় দিয়েছে তরুণ সহকর্মী, হাইকোর্টের সামনে শরৎ বসুর স্ট্যাচুর দিকে আপ্রাণ দৌড়ে জাপটে ধরেছে একজনকে। যাঁর মাঝারি গড়ন, গায়ে চাদর। এবং যিনি অতর্কিত আক্রমণে হতচকিত হয়ে চিলচিৎকার জুড়েছেন, ‘বাঁচাও, মার ডালা……!’
কী হল ব্যাপারটা? গাড়ি থেকে নেমে আমরাও ছুটলাম। কাছে গিয়ে দেখি, তরুণ সাব-ইনস্পেকটরের চোখেমুখে উত্তেজনা ঠিকরে বেরচ্ছে, হাঁফাতে হাঁফাতে বলছে, ‘পেয়েছি স্যার! এই ব্যাটাই স্টোনম্যান! কেমন বকের মতো লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটছিল! আমি ঠিক খেয়াল করেছি। বারে বারে ঘুঘু তুমি…’
থামিয়ে দিয়ে বকের মতো পা ফেলে হাঁটা ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালাম। এঁকে তো চিনি!
পোদ্দার কোর্টের কাছে একটা হার্ডওয়ারের দোকান চালান এই অবাঙালি ভদ্রলোক। নিতান্ত নিরীহ মানুষ। সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। দোষের মধ্যে, একটু লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটেন। বকের মতো।
ক্ষমা-টমা চেয়ে যখন ভদ্রলোককে বিদায় করছি চা খাইয়ে, তখনও তরুণ সহকর্মীর চোখেমুখে অবিশ্বাসের জ্যামিতি। এ-ও নয়?’
এ তো নয়ই, এখনও পর্যন্ত সন্দেহের বশে আটক হওয়া কেউই যে নয়, প্রমাণ মিলল বারো নম্বর খুনে। যেটা ঘটল এগারো নম্বরের ঠিক পাঁচদিন পরে, ২৬ ফেব্রুয়ারি। এবং এবার সমস্ত হিসেব উলটে দিয়ে ঘটনাস্থল তৃতীয় এবং নবম খুনের ঘটনাস্থলের গা ঘেঁষেই, শিয়ালদা ফ্লাইওভারের সাবওয়ের কাছে। ফের মুচিপাড়া থানা এলাকায়। একই জায়গায় সাধারণত বারবার আঘাত হানে না সিরিয়াল কিলাররা। সেই ট্র্যাডিশন বদলে দিল স্টোনম্যান। নিহত এবার এক পনেরো-ষোলোর হতভাগ্য কিশোর, যার পেশা বলতে ছিল স্টেশন-চত্বরে ভিক্ষাবৃত্তি। খুনের সময় মধ্যরাতের কিছু পরে। পদ্ধতি এক। খুনের অস্ত্রও এক। মৃতদেহের কয়েক হাত দূরে পড়ে থাকা রক্তলাল পাথর।
দুঃসময় চললে যা হয়, উটকো উপদ্রবেরও শেষ ছিল না তখন। এক রাতে হেস্টিংস থানা এলাকায় যেমন রাত আড়াইটে নাগদ দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে ওঠার মুখে এক যুবককে বসে থাকতে দেখল ‘পেট্রোলিং টিম’। বয়স তিরিশের নীচে। পরে আছেন দামি টি-শার্ট, ব্র্যান্ডেড জিন্স। সুদর্শন চেহারা। সঙ্গে একটা ব্যাগ।
—এখানে কেন? এত রাতে কী করছেন?
—স্টোনম্যান-কে ধরতে বেরিয়েছি। সপ্তাহে অন্তত দুটো রাতে নিয়মিত বেরই। ইউ ক্যান কল মি ‘stoneman catcher’.
বোঝো! স্টোনম্যানকে ধরতেই নাকানিচোবানির একশেষ। তার উপর স্টোনম্যানকে ধরতে বেরনো শখের গোয়েন্দাদেরও ধরতে হলে তো দুর্গতির বত্রিশকলা পূর্ণ। যুবকের সঙ্গের ব্যাগে পাওয়া গেল স্টিফেন হকিংয়ের ‘আ ব্রিফ হিস্ট্রি অফ টাইম’। এ ছাড়াও নাইলনের দড়ি-ক্ষুর-ছুরি, রুল, চওড়া বেল্ট এবং আরও কিছু ওষুধ টুকিটাকি।এগুলো কেন?
—বাহ্! স্টোনম্যানকে ধরতে গেলে এগুলো লাগবে না? তা ছাড়া স্টোনম্যানের আক্রমণে আহত কারও চিকিৎসাতেও তো লাগতে পারে।
কী আর বলার থাকে এর পর, নাম-ঠিকানা জেনে গাড়িতে তুলে দক্ষিণ কলকাতার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসা ছাড়া? বাড়িতে গিয়ে জানা গেল, যুবক মানসিক অসুস্থতায় ভুগছেন বেশ কিছুকাল। যুবকের মা-কে হাতজোড় করে হেস্টিংসের ওসি বলে এলেন, ‘মাসিমা, আমরা খুবই চাপের মধ্যে আছি। ছেলেকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাতে বাড়িতেই রাখার চেষ্টা করবেন প্লিজ়।’ আর যুবককে দিয়ে এলেন সহৃদয় পরামর্শ, ‘আমরা আর একটু চেষ্টা করি স্টোনম্যানকে ধরতে, না পারলে আপনার সাহায্য চাইব, কেমন?’
ন’মাসের মধ্যে এক ডজন খুন। কিনারাসূত্র অধরা। চেষ্টা তো হয়েছে সর্বস্ব নিংড়ে দিয়ে। কী করার থাকতে পারে আর? কিন্তু কে আর শুনতে চায় ব্যর্থ চেষ্টার ইতিবৃত্ত, কে শুনতে চায় ‘ভাল খেলিয়াও পরাজিত’-র কষ্টকথা? আসল তো ‘ফলেন পরিচয়তে।’ পুলিশের কাজ অপরাধীকে ধরা। সেটাই যখন পারছে না ন’মাস ধরে, কার সময় আছে ক্লান্তি-শ্রান্তি-পরিশ্রমের সাতকাহন শোনার?
রাজ্য প্রশাসন যখন পৌঁছে গিয়েছে অস্বস্তির চরমসীমায়, যখন কলকাতা পুলিশের সর্বস্তরে ঢালাও রদবদলের আলোচনা জমাট বাঁধছে রাইটার্সের অন্দরমহলে, তখনই, মার্চের প্রথম সপ্তাহের এক মধ্যরাতে ওসি এন্টালির ওয়ারলেস বার্তা ছড়িয়ে পড়ল লালবাজারের কন্ট্রোল রুম মারফত, ‘স্টোনম্যান কট রেড হ্যান্ডেড নিয়ার শিয়ালদা, বিইং ব্রট টু লালবাজার!’
স্টোনম্যান ধরা পড়েছে হাতেনাতে? অবশেষে? বারো পেরিয়ে তেরো নম্বর খুনের বেলায় খেল খতম? আনলাকি থার্টিন?
ফোন পাওয়া মাত্র ঊর্ধ্বশ্বাসে লালবাজার ছুটলেন গোয়েন্দাপ্রধান সহ ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের সমস্ত অফিসার। জানানো হল সিপি-কে। যিনি জানালেন, যত দ্রুত সম্ভব রওনা দিচ্ছেন।
প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছিলেন ওসি হোমিসাইড। গোয়েন্দাপ্রধানকে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান ওসি, ‘আসুন স্যার, বসুন।’
বসেন না গোয়েন্দাপ্রধান। একদৃষ্টে স্থির তাকিয়ে থাকেন চেয়ারে বসা পঞ্চাশ ছুঁইছুঁই স্মিতহাস্য মাঝারি গড়নের লোকটির দিকে। এ-ই স্টোনম্যান? এই লোকটা? যে শুধু লালবাজার নয়, পুরো শহরের ঘুম কেড়ে নিয়েছে গত নয় মাসে, সেই জুন থেকে? শান্তভাবে প্রশ্ন করেন গোয়েন্দাপ্রধান।
—কী নাম আপনার?
—কালীপদ দাস।
—বাড়ি কোথায়?
—রায়দিঘি। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা।
—কী করেন?
—রাজ্য সরকারের কর্মচারী স্যার।
—কোন ডিপার্টমেন্ট?
—ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ।
—পোস্টিং কোথায়?
—রানিবাঁধ, বাঁকুড়া। কিন্তু স্যার, আপনারা আমাকে ধরে এনেছেন কেন? কী করেছি আমি?
আর থাকতে পারেন না ওসি এন্টালি, ডিসি-ডিডি-র জেরার মাঝেই চেঁচিয়ে ওঠেন উত্তেজিতভাবে, কী করেছেন মানে? জানেন না কী করেছেন, জানেন না কী করতে যাচ্ছিলেন? হাতেনাতে ধরেছি স্যার, আর এখন বলছে কী করেছি…
হাতের ইশারায় ওসি-কে থামান গোয়েন্দাপ্রধান।
—অত উত্তেজনার কিছু নেই। কীভাবে ধরলেন এঁকে?
—স্যার, রোজকার মতো শিয়ালদা স্টেশনের আশেপাশে টহল দিচ্ছিলাম। ঘুরে দেখছিলাম ফুটপাথগুলো। বৈঠকখানা বাজারের কাছের ফুটপাথে চোখে পড়ে এঁকে। এক মহিলা গোঁ গোঁ করে চিৎকার করছিলেন, আর ঠিক তার পাশে শুয়ে থাকা এই ভদ্রলোক একটা পাথর দিয়ে মারতে যাচ্ছিলেন মহিলার মাথায়। ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরেছি। আর এখন বলছে, কী করেছি?
—পাথরটা কোথায়?
—এই যে স্যার…
একটা প্লাস্টিকের মোড়ক থেকে যেটা বার করলেন ওসি, সেটা পাথর নয়। খুব বেশি হলে একটু বড় সাইজ়ের থান ইট। আগের খুনগুলোয় একটাতেও ইটের ব্যবহার হয়নি। বারোটা খুনেরই অস্ত্র ছিল বড় পাথর, অন্তত পনেরো থেকে কুড়ি কেজি ওজনের। এই ইট দিয়ে মাথায় মারলে আঘাত লাগবে ঠিকই, কিন্তু প্রাণহানি একেবারেই নিশ্চিত নয়। তা হলে?
ফের জেরা শুরু করেন গোয়েন্দাপ্রধান।
—কলকাতায় কী করতে এসেছিলেন? পোস্টিং তো বললেন রানিবাঁধে। অফিসের কাজে এসেছিলেন?
—হ্যাঁ স্যার… তবে সেটা আসল কারণ নয়।
—তবে?
—ভাষণ শুনতে এসেছিলাম।
—ভাষণ মানে? কার ভাষণ?
—সুভাষবাবুর। ওঁর পরের সভাটা কবে কোথায় বলবেন প্লিজ়?
—সুভাষবাবু মানে?
—সুভাষবাবু স্যার! সুভাষচন্দ্র বসু। নেতাজি!
—নেতাজির ভাষণ?
—হ্যাঁ স্যার, শিয়ালদা স্টেশনের সামনে আজ নেতাজির সভা ছিল তো! অনেকদিনের ইচ্ছে, সামনে থেকে ওঁর ভাষণ শুনব। জীবন সার্থক হল আজ স্যার। ‘তোমরা আমাকে রক্ত দাও…… আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব…’ শুনতে শুনতে অন্য জগতে চলে যাচ্ছিলাম স্যার। গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল।
—বেশ তো! তা ভাষণ শেষ হওয়ার পর ফিরে গেলেন না কেন? শিয়ালদার ফুটপাথে রাত কাটাবেন বলে ঠিক করে এসেছিলেন?
—না না, তা কেন হবে স্যার? মিটিং শেষই তো হল রাত সাড়ে আটটায়। ট্রেনের গণ্ডগোল ছিল আজ। ফিরতে পারলাম না। ভাবলাম ভোরে ফিরব। রাতটা থেকে যাই রাস্তায়। এদিক-সেদিক ঘুরে ফুটপাথে শুয়ে পড়লাম। সবে ঘুমটা এসেছে, গোঁ গোঁ চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি এক মহিলা উঠে বসে আমাকে ঠেলছে। এমন আওয়াজ করছে মুখ দিয়ে, বাকিরাও জেগে গেল। আমি তখন থামানোর জন্য পাশে পড়ে থাকা ইট তুলে ভয় দেখাচ্ছিলাম, যাতে চুপ করে যায়…
কথার মাঝপথে ফের থামিয়ে দেন ওসি এন্টালি, ‘গল্প দিচ্ছে স্যার। মহা শয়তান! নেতাজির ভাষণ শুনতে এসেছিল! ইয়ার্কি মারার জায়গা পায়নি! কানের গোড়ায় দুটো দিলেই…’
ওসি এন্টালির দিকে এবার কড়া দৃষ্টিতে তাকান গোয়েন্দাপ্রধান, ‘আপনি থামবেন? আমি কথা বলছি তো!’
কালীপদকে নিয়ে লালবাজার থেকে গাড়ি রওনা দিল শিয়ালদায়, যেখান থেকে ওসি এন্টালি ধরেছিলেন ‘হাতেনাতে’। ততক্ষণে খবর ছড়িয়ে পড়েছে উল্কাগতিতে, ওই মাঝরাতেও। ‘স্টোনম্যান’ ধরা পড়েছে! গোয়েন্দাপ্রধানের নেতৃত্বে যখন টিম পৌঁছল শিয়ালদায়, ভিড় জমে গেছে সাংবাদিকদের। ভিড় জমে গেছে অন্তত শ’তিনেক কৌতূহলী জনতার। কন্ট্রোল রুম থেকে বাড়তি ফোর্স পাঠানো হয়েছে পরিস্থিতি আন্দাজ করে।
তথ্যতালাশে জানা গেল, কালীপদ মিথ্যে বলেননি। সহজেই চিহ্নিত করা গেল সেই মহিলাকে, যাকে মারতে গিয়েছিলেন কালীপদ। স্থানীয়রা জানালেন, বছর তিরিশের ওই মহিলা জন্মাবধি মূক ও বধির। সম্পূর্ণ অচেনা এক পুরুষ পাশে শুয়ে আছেন, এটা হঠাৎ আবিষ্কার করার পর আতঙ্কে গোঁ গোঁ করতে থাকেন। সেই আওয়াজে অন্য দু’-তিনজনেরও ঘুম ভেঙে যায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে মিলে গেল কালিপদর বয়ান।
‘নেতাজি’-র সভা? সেদিন একটি রাজনৈতিক সংগঠনের সভা সত্যিই ছিল শিয়ালদা চত্বরে। শেষ হয়েছিল রাত আটটার পর। এবং সত্যিই সেদিন যান্ত্রিক গোলযোগে রাত সোয়া এগারোটা অবধি শিয়ালদা লাইনে ট্রেন বন্ধ ছিল।
লোকটা তা হলে গল্প বানাচ্ছে না? স্রেফ মনোবিকার গ্রস্ত? ভোরেই দুটো টিম রওনা দিল রায়দিঘিতে কালীপদর বাড়িতে এবং রানিবাঁধের অফিসে। বিস্তর খোঁজখবর করে যা জানা গেল, এরকম।
যখন যুবক, সবে চাকরিতে ঢুকেছেন, তখন থেকেই মাথার ব্যামো দেখা দিয়েছিল কালীপদর। কখনও একেবারে স্বাভাবিক আচরণ করতেন, কখনও আবার চলে যেতেন অন্য দুনিয়ায়। ‘হ্যালুশিনেশনস’ হত, টাইমমেশিনে পিছিয়ে গিয়ে নিজেকে কখনও ভাবতেন আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্য, কখনও বা বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সেনানী।
ডাক্তারবদ্যি দেখিয়েছিলেন বাড়ির লোকেরা। উন্নতি হয়নি বিশেষ। অফিসে হয়তো এক সপ্তাহ মন দিয়ে কাজ করলেন আর পাঁচজন সহকর্মীর সঙ্গে, হঠাৎ পরের সপ্তাহে কাউকে কিছু না বলে দুম করে চলে গেলেন কলকাতা বা অন্য কোথাও। বাড়ির এবং অফিসের লোকেরা ক্রমে মানিয়ে নিয়েছিলেন এই খ্যাপাটে স্বভাবের সঙ্গে।
অফিসের হাজিরাখাতা খুঁটিয়ে দেখা হল গত ন’মাসের। খোঁজ নেওয়া হল গ্রামের বাড়িতেও, খুনগুলোর সঙ্গে দিন মিলিয়ে মিলিয়ে। এবং দেখা গেল, আগের খুনগুলোর দিন হয় অফিস করেছিলেন, নয় বাড়িতে ছিলেন। কোনওভাবেই কলকাতায় আসার সম্ভাবনা ছিল না।
আরও নিঃসংশয় হতে নেওয়া হল পায়ের ছাপ। মিলল না বেকবাগানের খুনের জায়গার থেকে সংগৃহীত ফুটপ্রিন্টের সঙ্গে। না, ইনি নন। স্টোনম্যান অধরাই।
এবং অধরাই রয়ে গেল কলকাতা পুলিশের ইতিহাসে দগদগে ক্ষতচিহ্ন রেখে। তেরো নম্বর খুনটা আর হয়নি, কে জানে কীভাবে, হঠাৎই থেমে গিয়েছিল রাতের সিরিয়াল-কিলিং। ‘স্টোনম্যান’ কে, সেই রহস্যকে রহস্যাবৃতই রেখে।
কে ছিল স্টোনম্যান? ধরতে পারিনি আমরা। জানতে পারিনি আমরা। যেমন জানতে পারিনি, ‘স্টোনম্যান’ না ‘স্টোনমেন’? এক, না একাধিক? একক বিকার, না কোন চক্রের অঙ্গুলিহেলন? তবে স্বাভাবিক বুদ্ধি যা বলে, তার সঙ্গেই সহমত ছিলেন তদন্তকারী অফিসারদের সংখ্যাগরিষ্ঠ। ‘স্টোনম্যান’ একজনই ছিল। খুনগুলো করে মনোবিকার চরিতার্থ করা ছাড়া কোনওরকম জাগতিক লাভ হয়নি ঘাতকের। একাধিক সদস্যবিশিষ্ট কোনও চক্রের জড়িত থাকার সম্ভাবনা এই জাতীয় সিরিয়াল-হত্যায় ক্ষীণতমই।
বলা হয়, অপরাধী সে যতই ক্ষুরধার মস্তিষ্কের হোক না কেন, হোক না যতই ধুরন্ধর, কিছু না কিছু চিহ্ন ছেড়ে যায়ই কোথাও না কোথাও, যা মৃত্যুবাণ হয়ে দাঁড়ায় ভবিষ্যতে, আইন যার উপর ভর দিয়ে পৌঁছে যায় অপরাধীর দোরগোড়ায়। বলা হয়, ‘পারফেক্ট ক্রাইম’ বলে নাকি কিছু হয় না। ভুল। হয়, পারফেক্ট ক্রাইমও হয়।
স্টোনম্যান জানিয়েছিল।