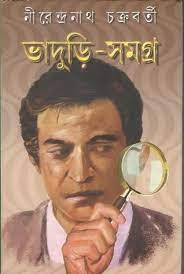- বইয়ের নামঃ ভাদুড়ি সমগ্র
- লেখকের নামঃ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
- প্রকাশনাঃ দে’জ পাবলিশিং (ভারত)
- বিভাগসমূহঃ গোয়েন্দা কাহিনী
বিগ্রহের চোখ
বিগ্রহের চোখ – গোয়েন্দা ভাদুড়িমশাই – নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
আজ এগারোই এপ্রিল, রবিবার। কৌশিককে সঙ্গে নিয়ে ভাদুড়িমশাই একটা তদন্তের কাজে বাঙ্গালোর থেকে দিন কয়েকের জন্য কলকাতায় এসেছেন। ফলে অরুণ স্যানালের কাকুড়গাছির ফ্ল্যাটে আজ ছুটির দিনের আজ্ঞা একেবারে জমজমাট। ঘড়িতে এখন সকাল দশটা বাজে। কিন্তু দুপুরের খাওয়াটা যেহেতু আমরা আজ এখানেই সেরে নেব, তাই আমারও বাড়ি ফেরার তাড়া নেই, সদানন্দবাবুরও না। তার উপরে আবার গতকাল রাত্তিরে যখন ভাদুড়িমশাইয়ের সঙ্গে টেলিফোনে আমাদের কথা হয়, সদানন্দবাবু তখন তাকে মনে করিয়ে দিতে ভোলননি যে, বাংলা বছরের এটাই হচ্ছে লাস্ট সানডে। কথাটার মধ্যে যে একটা গূঢ় ইঙ্গিত ছিল, ভাদুড়িমশা, সেটা ধরতে পেরেছে ঠিকই, তা নইলে আর টেলিফোনের মধ্যেও অমন হোহো করে তিনি হাসতে থাকবেন কেন? সুতরাং আশা করা যাচ্ছে যে, আজকের দ্বিপ্রহরিক খাওয়াটা বেশ ঢালাও রকমেরই হবে।
আড্ডা জমে যাবার অবশ্য আরও দুটো কারণ আছে। তার মধ্যে প্রথম কারণ হল, কৌশিকের চোখ এই সময় টিভির পর্দায় টি, এ. টির কার্টুন পিকচার্সে আটকে থাকার কথা, কিন্তু কলকাতার কেবল অপারেটররা যে-সব পে-চ্যানেলের ছবি দেখানো বন্ধ করে দিয়েছে, তার একটা হচ্ছে টি.এন.টি। কৌশিকও তাই টেলিভিশনের সুইচ অন করেনি, এবং কার্টুন ছবির হুল্লোড় বন্ধ থাকায় একদিকে যেমন শব্দ দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে, অন্যদিকে তেমনি আমাদের আড্ডাতেও কোনও ব্যাঘাতের সৃষ্টি হচ্ছে না। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে সদানন্দবাবুর গল্প। গল্পটা ক্রমে-ক্রমে যেদিকে মোড় নিচ্ছে, তাতে মনে হয়, খুব শিগগিরই একটা রোমহর্ষক ঘটনা ঘটবে।
ঘটলও। সদানন্দবাবু বললেন, “আপনাদের আমি অনেক দিন ধরে দেকচি তো, যেমন কিরণবাবু, তেমনি এ-বাড়িরও কাউকে চিনতে আমার বাকি নেই, তেলপড়া, জলপড়া, তুকতাক, ঝাড়ফুক, বাটি চালান, ক্ষুর চালান কি ওই রকমের কিছুই যে আপনারা বিশ্বেস করেন না, মুক টিপে হাসেন আর মনে-মনে আমাকে একটা ড্যাম লায়ার ভাবেন, সে আমি খুব ভালই জানি। কিন্তু আমি তো নিজের চোকে দেকিচি, তাই কী করে অবিশেস করব বলুন?”
অরুণ সান্যাল বললেন, “আহা-হা, কী হল বলুন না, বাটিটা একটা ফ্লাইং সসার হয়ে আকাশে উড়ে গেল?”
“তা কেন উড়বে?” সদানন্দবাবু বললেন, “না না, তা ওড়েনি, কিন্তু যা হল, সেও চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। এই দেকুন, আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। বাটিটা তো এতক্ষণ নীলকণ্ঠ ঘোষের উঠোনের ওপরে একটা জিগজ্যাগ কোর্সে ঘোরাফেরা করছিল, হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, দুম করে একেবারে….ওরে বাবা রে বাবা, সে এক বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড মশাই….ওই যাকে আপনারা বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা হয় না বলেন আর কী, সেই রকমের আনবিলিভেবল ইনসিডেন্ট!”
ভাদুড়িমশাই মিটিমিটি হাসছিলেন। বললেন, “খেলে যা! কী হল, সেইটে বলুন দেখি।”
“বলচি, বলছি।” সদানন্দবাবু বললেন, “বেন্দাবন মাঝির যে বাটি এতক্ষণ নীলকণ্ঠ ঘোষের কাঁচারি-ঘরের সামনেকার উঠোনের উপর হরাইজন্টালি ঘোরাফেরা করছিল, সেটা হঠাৎ ভার্টিক্যালি মাটির থেকে তা ধরুন দু-আড়াই ফুট নাপিয়ে উটে অ্যাব্রাগুলি একটা টার্ন নিয়ে কোতায় গিয়ে আটকে গেল জানেন?”
কৌশিকের চোখ দুটো দেখে মনে হচ্ছিল, কোটর থেকে যে-কোনও মুহূর্তে তারা বেরিয়ে আসবে। সোফা থেকে একটুখানি সামনে ঝুঁকে ঘড়ঘড়ে গলায় সে জিজ্ঞেস করল, “কোথায়?”
“নীলকণ্ঠের বুড়ি-শাশুড়ির মাজায়!”
“অ্যাঁ?” অরুণ সান্যাল প্রায় আঁতকে উঠে বললেন, “বাটিটা আর জায়গা পেল না? অব অল প্লেসেস…”
সদানন্দবাবু বললেন, “ইয়েস, মাজা! কী বলব মশাই, বুড়ি তো হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল! কিন্তু যতই না কেন চেঁচাক, আর মাজা থেকে ঝেড়ে ফেলার জন্যে টানা হাচড়া করুক, বাটি আর খোলে না! খুলবে কী করে, এ হল গে বেন্দাবন মাঝির বাটি! দশ-দশখানা গায়ের মধ্যে অমন গুনিন তো দুটি নেই! মন্তর পড়ে দিয়ে চালান করেছে কিনা, তাই চোরের মাজায় একেবারে জম্পেশ হয়ে সেঁটে আচ্চে। তো এই হচ্ছে ব্যাপার?”
কৌশিক বলল, “তার মানে নীলকণ্ঠ ঘোষের সোনা-বাঁধানো নস্যির ডিবে তার শাশুড়িই চুরি করেছিল?”
“তা করেছিল বই কী।“ সদানন্দবাবু বললেন, “অতি ধুরন্ধর জাঁহাবাজ মহিলা! তার উপরে ক্লিপ…ক্লিপ…ওই যে কী একটা কতা রয়েছে…”
“ক্লেপটোম্যানিয়াক?”
“রাইট! যেখেনেই যাক, হাতের কাঁচে দামি কিছু পেলেই হল, হাপিস করে দেবে।”
“নীলকণ্ঠ ঘোষ তা জানত।”
“অফ কোর্স জানত।” সদানন্দবাবু বললেন, “কিন্তু তার বউ সেকতা বিশ্বেস করত । বলত, ছিছি, মেয়ে-জামাইকে ভালবাসেন বলে বরাবরের জন্যে বেড়াতে এয়েছেন, আর তার নামে কিনা যা-তা সব বলচ। নীলকণ্ঠও এই নিয়ে আর কতা বাড়ায়নি। কিন্তু শেষকালে নস্যির ডিবে চুরি যেতে সে আর চুপ করে থাকতে পারল না….বেন্দাবনকে ডেকে পাটাল।”
অরুণ সান্যাল বললেন, “তা উদ্ধার হল সেই নস্যির ডিবে?”
সদানন্দবাবু বললেন, “হল বই কী, বাটি যেখেনে আটকে গে, সেখেন থেকেই হল। বুড়ির মাজায় ছিল থান-কাপড়ের কষির গিট, সেই গিঁটের ভেতর থেকেই নস্যির ডিবে বেরিয়ে পড়ল। সোনার পাতে মোড়া কষ্টিপাথরের ডিবে, তার ডালায় আবার পায়রার চোকের মতো টকটকে লাল চুনি বসানো, সে মানে দ্যাকবার মতো জিনিস।”
“তা কাপড়ের গিঁট থেকে জামাইয়ের নস্যির ডিবে বেরোতে বুড়ি কিছু বলল না?”
“বলল বই কী। বলল যে, সে যখন ঘুমুচ্ছিল, তখন জামাই-ই নির্ঘাত তার কাপড়ে ওটা বেঁদে রেকে গ্যাচে। চোর অপবাদ দিয়ে তাড়াতে চায় আর কী।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “তা বিদেয় হল শাশুড়ি?”
“তা-ই কখনও হয়?” সদানন্দবাবু বললেন, “নীলকণ্ঠের বউ দুগগামণি রয়েছে না? সে অমনি চোক পাকিয়ে বলল যে, মা’কে বিদেয় করলে সে আত্মঘাতী হবে, তারপর পেত্নি হয়ে নীলকণ্ঠর ঘাড় মটকাবে।”
“বাস্, নীলকণ্ঠ তাতেই কাত?”
“তাতেই কাত।” সদানন্দবাবু বললেন, “কাত না হয়ে উপায় কী! একে তো ব্যাটা ঘোর হেন-পেড, বউয়ের কতায় ওটে-বসে, তায় আবার অ্যায়সা ভূতের ভয় যে, সন্ধের পরে যতই ডাকাডাকি করুন, বাড়ির বাইরে বেরুবে না, যা বলার তা ওই ভেতর থেকেই বলবে।”
“শাশুড়ি-ঠাকরুন অতএব রয়েই গেল?”
“রয়েই গেল। তবে কিনা.. মানে এরপরে যা রটে গেল, সেই কাণ্ডটা তো আর আমার নিজের চোখে দ্যাকা নয়….নেহাতই শোনা কতা..তাই আপনারা বিশ্বেস করতেও পারেন, না-ও পারেন। তবে হ্যাঁ, যা রটে, তার সবটা না হোক, খানিকটে তো বটেই।”
“কী রটেছিল?”
“রটে গেল যে…মানে..” সদানন্দবাবু গলাটা একটু খাকড়ে নিয়ে বললেন, “এই ঘটনার পর থেকে রাত্তিরে ঘুমুবাব সময়েও নীলকণ্ঠ ঘোষ নাকি তার বাঁদানো দাঁতের পাটি খুলে রাখত না।”
কৌশিক বলল, “কেন, কেন?”
“সোনা দিয়ে বাঁদানো দাঁত তো।” সদানন্দবাবু বললেন, “নীলকণ্ঠের তাই ভয় ধরে গেল যে, দাঁতের পাটি খুলে যদি ঘুমোয়, তো শাশুড়ি সেটাও হাপিস করে দেবে।”
শুনে আমরা সবাই হো-হো করে হেসে উঠলুম। কিন্তু সদানন্দবাবু হাসলেন না। বললেন, “হাসছেন হাসুন, কিন্তু আসল কতাটা ভুলে যাবেন না। বেন্দাবন মাঝির বয়েস অ্যাদ্দিনে নব্বই ছাড়িয়েছে, কিন্তু সে মরে যায়নি। বলেন তো তাকে খবর পাটিয়ে আনিয়ে নেওয়া যায়।”
অরুণ সান্যাল বললেন, “তাকে আনিয়ে কী হবে?”
“বাঃ, ভাদুড়িমশাই যাদের ধরতে বেরিয়েছে, সেই চোরগুলোকে ধরতে হবে না?”
“বেন্দাবন মাঝি এসে চোর ধবে দেবে?”
“আহাহাহাহা, সদানন্দবাবু অসহিষ্ণু গলায় বললেন, “কতাটা দেকছি আপনারা ধরতেই পারেননি। বেন্দাবন কেন চোর ধরবে? দারোগাবাবু কি কক্ষনো নিজের হাতে চোর ধরে? চোর ধরে তার সেপাইগুলো। তা বিবেচনা করুন যে, বেন্দাবন হচ্চে গিয়ে দাবোগাবাবু। কিন্তু তার তো সেপাই-টেপাই নেই। থাকার মদ্যে আচে ওই বাটি।”
“বুঝেছি।” কৌশিক বলল, “ওই বাটি গিয়ে চোর ধরবে। নীলকণ্ঠ ঘোষের শাশুড়িকে যেমন ধরেছিল।…কী, ঠিক বুঝেছি তো?”
“কিচুই বোজোনি।” সদানন্দবাবু বললেন, “বাটি কি আর এমনি-এমনি চোর ধরবে নাকি? তার মদ্যে মন্তর পড়ে দিতে হবে না? বাটি-চালানের ওটাই হচ্ছে আসল কতা, ওই মন্তর। অবিশ্যি ভাদুড়িমশাই যদি চান তো বাটির বদলে ক্ষুর কি কাটারি-চালানের ব্যবস্থাও করা যায়। কিন্তু সেটা একটু রিস্কি ব্যাপার।”
“রিস্কি বলছেন কেন?”
কৌশিকের প্রশ্নের উত্তরে সদানন্দবাবু সস্নেহ হাস্য করলেন। তারপর বললেন, “বোকা ছেলে! এই সহজ কতাটাও বুজতে পারলে না? আরে বাবা, ক্ষুর কি কাটারি চালান করলে সে তো আর বাটির মন কারও মাজায় কি অন্য কোতাও গিয়ে সেঁটে বসবে না, কালপ্রিটের গলা অব্দি নাপিয়ে উটে আপনা থেকেই কোপ ঝেড়ে দেবো। না না, সে-সব রক্তারক্তি ব্যাপারের মদ্যে গিয়ে কাজ নেই। তার উপরে আবার মস্তরে ভুল থাকলে কালপ্রিটের বদলে অন্য কারও গলাতেও কোপ ঝেড়ে দিতে পারে। সে তো কেলেঙ্কারির একশেষ। তার চে বাটি-চালানই ভাল। ইন ফ্যাক্ট, ভাদুড়িমশাইকে সেই জন্যেই অ্যাডভাইস দিচ্ছিলাম যে, উনি বরং বাটি-চালানের ব্যবস্থা করুন। তা উনি গাই করচেন না।”
ভাদুড়িমশাইয়ের কাজের সূত্রেই কথাটা উঠেছিল বটে। কাজটা তদন্তের, এবং তদন্তটা চুরির।
এ সম্পর্কে ভাদুড়িমশাইয়ের কাছে যা শুনেছিলাম, সেটা খুব সংক্ষেপে বলছি। ভারত জুড়ে কারবার চালায়, এমন একটা মিউঁচুয়াল ফান্ড তাদের বাঙ্গালোরের সদর দফতর থেকে দেশের হরেক জায়গায় যে ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট পাঠায়, কলকাতার আমানতকারীদের অনেকের কাছেই তা ইদানীং পৌঁছচ্ছিল না। মাঝপথেই উধাও হয়ে যাচ্ছিল সেগুলি। শুধু তা-ই নয়, হরেক ব্যাঙ্কে ভুয়ো অ্যাকাউন্ট খুলে ওয়ারেন্টগুলি ভাঙিয়েও নেওয়া হচ্ছিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ধরা যাচ্ছিল না, ঠিক কোন পয়েন্ট থেকে সেগুলি নিখোঁজ হচ্ছে। ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্টগুলি ডাকে ফেলার পরে, না কোম্পানির আপিস থেকে সেগুলি ডাকঘরে পৌঁছে দেবার আগেই। গোটা ব্যাপারটা নিয়ে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয় চারু ভাদুড়ি ইনভেস্টিগেশনসকে। কোম্পানি থেকে যদিও শুধু ডাক বিভাগকে সন্দেহ করা হচ্ছিল, কিন্তু কাজটা হাতে নেবার পর হপ্তাখানেকের মধ্যেই ভাদুড়িমশাই বুঝতে পেরে যান যে, কোম্পানির ভিতরেই রয়েছে একটা দুষ্টচক্র, ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট হাপিস করা ও ব্যাঙ্কে জাল নামে জাল অ্যাকাউন্ট খুলে ঝটপট সেগুলো ভাঙিয়ে নেবার ব্যাপারে যাদের ভূমিকা একটা আছেই। কোম্পানির কলকাতা-আপিসের ডেসপ্যাঁচ-বিভাগের খাতাপত্র খুঁটিয়ে দেখে তার ধারণা আরও জোর পেয়ে যায়। সেই অনুযায়ী একটা রিপোর্টও তিনি তৈরি করে ফেলেছেন। বাঙ্গালোরে ফিরে কোম্পানির হেড আপিসে সেটা তিনি সাবমিট করবেন।
শুনে সদানন্দবাবু বললেন, “তা তো হল, কিন্তু চোরগুলো ধরা পড়বে তো?”
“পড়বে বলেই তো আশা করছি,” ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, “তবে কিনা চুরিটা যে বন্ধ হবে, আপাতত সেটাই বড় কথা। অবিশ্যি আমার রিপোর্ট অনুযায়ী যদি কাজ
কথাটা শুনে সদানন্দবাবু যে খুব খুশি হয়েছেন, তা মনে হল না। বেজার গলায় বললেন, “আমি হলে কিন্তু ফাস্ট অব অ ওই চোরগুলোকেই ধরে ফেলতুম মশাই।”
অরুণ সান্যাল বললেন, “কী করে ধরতেন?”
এই প্রসঙ্গেই এসেছিল বাটি চালানের কথা। সদানন্দবাবু হেসে বলেছিলেন, “সেটা তো অতি সহজ কাজ, মশাই। স্রেফ বেন্দাবন মাঝিকে ডাকিয়ে এনে বলতুম, বাটি চালাও!”
অরুণ সান্যাল গল্পের গন্ধ পেয়ে গিয়েছিলেন। অপ্রাকৃতে বিন্দুমাত্র বিশ্বাস না থাকা সত্ত্বেও মুখেচোখে নকল কৌতূহল ফুটিয়ে বললেন, “বেন্দাবন মাঝি? হু ইজ হি? আ বোটম্যান?”
কৌশিক বলল, “অ্যান্ড হোয়াট ডাজ হি ডু উইথ আ বাটি?”
“বেন্দাবন ইজ অ্যান ওঝা।” সদানন্দবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, “আর ওই বাটি হচ্চে তার ওয়েপন। তার বাটি চালানের ওস্তাদি তত আপনারা দ্যাকেননি। দেকলে আর মশকরা করতে হত না, সব্বাই থ মেরে যেতেন। ওরে বাবা রে বাবা, সে তো হুলুস্থুল কাণ্ড মশাই!”
বাস, শুরু হয়ে গেল বাটি চালানের গল্প। যে-গল্পের আদ্যন্ত আমরা একটু আগেই শুনেছি।
তা গল্প এক সময়ে শেষ হল। দু’চারটে কথাও হল তা-ই নিয়ে। অরুণ সান্যাল আর ভাদুড়িমশাই এমন দু’চারটে খোঁচা-মারা মন্তব্য করলেন, যাতে বোঝা গেল যে, বেন্দাবন মাঝির ভয়াবহ সব কীর্তিকলাপের একটি বর্ণও তারা বিশ্বাস করেননি। কৌশিক অবশ্য তার বাপ কিংবা মামার মতো গল্পটাকে একেবারে তুড়ি মেরে উড়িয়ে না দিয়ে বলল, “কী জানি বাবা, হতেও পারে।”
সদানন্দবাবু তাতে আরও রেগে গিয়ে বললেন, “হতে পারে কী হে, হয়েছিল। বলো তত বেন্দাবনকে ডেকে পাটাই, সে এসে নিজের মুকে সব বলুক। তা হলে তো বিশ্বেস হবে?”
কৌশিক এর উত্তরে কী বলত, তা আর শোনা হল না, কেন না সেই মুহূর্তে ফ্ল্যাটের কলিং বেল বেজে উঠল, আর তার একটু বাদে এ বাড়ির কাজের মেয়েটি এসে বলল, “একজন বাবু এয়েছেন, মামাবাবুর সঙ্গে দ্যাক করতে চান।”
.
॥ ২॥
কাজের মেয়েটি যে-ভদ্রলোকটিকে সঙ্গে করে ড্রয়িং রুমে পৌঁছে দিয়ে গেল, পঞ্চাশ থেকে পঁচাত্তরের মধ্যে যে-কোনও বয়সই তার হতে পারে। এই রকমের চেহারা আকছার চোখে পড়ে না, এইরকমের পোশাকও না। মানুষটি লম্বা প্রায় ফুট ছয়েক। শরীর অতিশয় কৃশ ও দড়ি-পাকানো টাইপের। মাথার সামনের দিকের চুল উঠে যাওয়ায় খুলির অনেকখানি অংশ কপালের দখলে এসে গেছে। মাথার বাদবাকি অংশের চুলের গোড়ার দিকটা সাদা, উপরের দিকটা লালচে। তাতে মনে হয়, ভদ্রলোক কলপ ব্যবহার করতেন, কিন্তু, যে-কোনও কারণেই হোক, এখন আর করেন না। গালের হাড় উঁচু। রং ফর্সা, কিন্তু ফ্যাকাশে। খাড়া নাকের নীচে পাকানো গোঁফ। গোঁফের দুই প্রান্তদেশ ছুঁচোলো ও ঊর্ধ্বমুখী। দৃষ্টিপাতের ধরনে কিছুটা সন্দেহের সঙ্গে খানিকটা আত্মম্ভরিতাও মিশে আছে। অক্ষিতারকা নীলবর্ণ, কিন্তু কিঞ্চিৎ ঘোলাটে। চোখের কোলে যে-পরিমাণ কালি জমেছে, তাতে রাত্রি-জাগরণের ছাপ স্পষ্ট। একই সঙ্গে সন্দেহ হয় যে, ইনি খুব একটা সুশৃঙ্খল ও নিয়মনিষ্ঠ জীবন যাপন করেন না।
ভদ্রলোকের পায়ে শুড়হোলা লপেটা। পরনে চুনোট করা কচি ধুতি ও ঊর্ধ্বাঙ্গে একটু লম্বা ঝুলের বর্ডার বসানো হালকা গোলাপি রঙের মেরজাই। হাতে রুপোবাঁধানো পাতলা ছড়ি। মেরজাইটিতে বোতাম নেই, সেটি বুকের একপাশে ফিতে দিয়ে বাঁধা। সব মিলিয়ে উনিশ শতকের কাপ্তান বাবু বলে ভ্রম হয়। এমনও সন্দেহ হয় যে, দীনবন্ধু মিত্রের ‘সধবার একাদশী’ কি অমৃতলাল বসুর ‘বিবাহ বিভ্রাট’ নাটকে অভিনয় করতে করতে ইনি রঙ্গালয় থেকে সরাসরি এখানে চলে এসেছেন। কিন্তু তার আগে সাজঘরে ঢুকে পোশাকটা পালটে আসেননি।
বুকের কাছে আড়াআড়ি করে ধরা ডান হাতের কব্জির উপর দিয়ে কোঁচার প্রান্তদেশ ঝুলিয়ে দেওয়া, ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে অরুণ সান্যালের ইঙ্গিত অনুযায়ী সামনের সোফায় বসেই একটা ভুল করে বসলেন। ডান হাতের ছড়ির ডগাটি ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে তুলে ধরে বললেন, “কাগজে আপনাব ছবি দেখেছি। আপনি নিশ্চয় মিঃ চারু ভাদুড়ি?”
ভাদুড়িমশাই তক্ষুনি তার প্রশ্নের জবাব দিলেন না। একেবারে স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর কেটে-কেটে, প্রতিটি শব্দকে পৃথকভাবে উচ্চারণ করে বললেন, “আপনি কি এইভাবেই সকলের সঙ্গে কথা বলেন নাকি?”
ভদ্রলোক যে হকচকিয়ে গেছেন, সেটা তার মুখচোখ দেখেই আমরা বুঝতে পারছিলাম। একটু বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে বার দুয়েক ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়ে বললেন, “আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না। এইভাবে মানে?”
“এইভাবে মানে যাঁর সঙ্গে কথা বলছেন তার দিকে ছড়ি উঁচিয়ে বলেন?”
ভদ্রলোকের বিভ্রান্ত ভাব তখনও কাটেনি। বললেন, “আজ্ঞে হ্যাঁ, এইভাবেই তো বলি।”
“আর বলবেন না।” ভাদুড়িমশাই ঈষৎ হেসে বললেন, “বাড়িতে চাকরবাকরদের সঙ্গে যদি-বা বলেন, বাড়ির বাইরে কারও সঙ্গে বলবেন না।”
“কেন, এতে দোষ হয়?”
“আমার ধারণা, হয়। আর কথা যখন আমার সঙ্গে, তখন আমার যেটা ধারণা, সেই অনুযায়ী আপনাকে কথা বলতে হবে।….দিন, ছড়িটা আমাকে দিন।”
হাত বাড়িয়ে ভদ্রলোকের হাত থেকে ছড়িটা নিয়ে নিলেন ভাদুড়িমশাই। তারপর বললেন, “হ্যাঁ, আমিই চারু ভাদুড়ি। কিন্তু আপনাকে তো চিনতে পারলুম না।”
ছড়ি বেহাত হওয়ায় ভদ্রলোকের ব্যক্তিত্ব একটু চুপসে গিয়ে থাকবে। তার কণ্ঠস্বর থেকেই সেটা বোঝা গেল। নিচু গলায় বললেন, “আমার নাম বিমলভূষণ সেন।”
‘বিমলভূষণ…বিমলভূষণ…” নামটাকে ঈষৎ অস্পষ্টভাবে বার দুয়েক উচ্চারণ করলেন ভাদুড়িমশাই, তারপর বললেন, “নামটা চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। আচ্ছা, মার্চের শেষে আপনিই কি আমাকে বাঙ্গলোরে ফোন করেছিলেন?”
“আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই করেছিলুম,” বিমলভূষণ বললেন, “কিন্তু তখন আপনি দিল্লিতে ছিলেন, তাই কথা হয়নি। তবে কিনা বাঙ্গালোর থেকেই আমাকে বলা হয়েছিল, দিল্লি থেকে আপনি আর বাঙ্গালোরে ফিরবেন না, ওখানকার কাজ সেরে এপ্রিলের গোড়ায় কলকাতায় চলে আসবেন।”
“ঠিক বলেনি। দিল্লি থেকে একদিনের জন্যে বাঙ্গালোরে ফিরেছিলাম, তারপর সেখান থেকে কলকাতায় আসি। ইন ফ্যাক্ট, বাঙ্গালোরে ফিরেছিলুম বলেই আপনার কথা জানতে পারি। তো আপনার সমস্যা তো একটা হিরে নিয়ে, তাই না?”
“একটা নয়, দুটো হিরে।” বিমলভূষণ বললেন, “কিন্তু আপনার কলকাতার কাজ কি মিটেছে?”
“গতকালই মিটেছে। কিন্তু তাই বলে যে এক্ষুনি বাঙ্গালোরে ফিরব, তাও নয়। অনেক দিন বাদে এলুম তো, হাতে বিশেষ জরুরি কাজও নেই, তাই দিন কয়েক এখানে কাটিয়ে যাব ভাবছি।”
একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন ভাদুড়িমশাই, তারপর বললেন, “কিন্তু আমার কলকাতার ঠিকানা পেলেন কোথায়? বাঙ্গালোর আপিস থেকেই জানিয়েছিল?”
“আজ্ঞে হ্যাঁ। ওরাই বলেছিল যে সম্ভবত দশ তারিখের পর থেকে আপনি একটু ফ্রি থাকবেন।”
“তাই আর কোনও ফোন-টোন না করে সরাসরি চলে এসেছেন?”
“আজ্ঞে হ্যাঁ।” বিমলভূষণের চোখেমুখে যে একটা আত্মম্ভরিতার ছাপ দেখেছিলুম, খানিক আগেই সেটা চলে গিয়ে একটা হীনম্মন্যতার ভাব এসে গিয়েছিল। বললেন, “তবে আমাদের আদি বাড়ি তো চন্নননগরে, সেখান থেকে আসিনি। আসলে বাগবাজারেও একটা বাড়ি আছে আমাদের, অবিশ্যি সেখানে কেউ থাকে না, ওই যা আমিই মাঝে-মধ্যে এসে দু’চারদিন কাটিয়ে যাই, আপাতত সেখান থেকেই আসছি।”
“বাঙ্গালোরে ফোনটা করেছিলেন কোথা থেকে?”
“চন্নননগর থেকে।” বিমলভূষণ বললেন, “ওই যে বললুম, ওখানেই আমাদের আদিবাড়ি। মন্দিরও ওখানেই। মন্দির আমার প্রপিতামহ কালীভূষণ সেন বানিয়েছিলেন। বিগ্রহও তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন।…কেন, বাঙ্গালোরে যিনি ফোন ধরেছিলেন, তাঁকে তো আমি সবই বলেছি। তার কাছে আপনি কিছু শোনেননি?”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “শুনেছি। কিন্তু তখন তো আমার কলকাতায় আসার তাড়া ছিল। তাড়াহুড়োর মধ্যে শুনেছি বলে সব কথা আমার ভাল মনে নেই। আপনি বরং গোড়া থেকে সবটা আবার বলুন।”
বিমলভূষণ অতঃপর যা বললেন, তার মধ্যে আগাছা বিস্তর, অপ্রয়োজনীয় ডালপালাও নেহাত কম নয়, সে-সব হেঁটে ফেললে মোদ্দা ব্যাপারটা যা দাঁড়ায়, সেটা এইরকম :
কালীভূষণ ছিলেন ধনাঢ্য ভূস্বামীর একমাত্র সন্তান। পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে যে বিত্ত ও জমিজমা পেয়েছিলেন, নিজের বুদ্ধিবলে তিনি তা আরও বাড়িয়ে নেন। চন্দননগর ফরাসিশাসিত এলাকা, তাই ফরাসি পক্ষের সঙ্গে তিনি সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন; অন্যদিকে, চন্দননগরের চৌহদ্দির বাইরেও বিস্তর জমিজমা ছিল বলে ইংরেজদেরও পারতপক্ষে চটাতেন না। কালীভূষণের জন্ম ১৮৪০ সালে। বাল্যবয়সে বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু তার বয়স যখন আটত্রিশ ও স্ত্রী শান্তিলতার তেত্রিশ, তখনও পর্যন্ত তাদের কোনও সন্তানাদি না হওয়ায় কালীভূষণ ধরেই নিয়েছিলেন যে, কোনও উত্তরাধিকারী না রেখেই তাকে ইহলোক থেকে বিদায় নিতে হবে। মোটামুটি সেই সময়েই এক রাত্রে তিনি একটি শিবমন্দির স্থাপনের জন্য স্বপ্নাদিষ্ট হন। স্বপ্নাদেশ পালনে দেরি হয়নি। চন্দননগরে তার বসতবাড়ির সংলগ্ন জমিতে ১৮৮০ সালেই তিনি মন্দির নির্মাণ করিয়ে তাতে হরপার্বতীর মূর্তি স্থাপন করেন। এর পরে-পরে যা ঘটে, স্বপ্নাদেশ পালনের সঙ্গে তার কোনও কার্যকারণের যোগ আছে কি না, বলা শক্ত, কিন্তু ঘটনা এই যে, এতকাল যাঁকে বন্ধ্যা রমণী বলে ভাবা হয়েছিল, সেই শান্তিলতা এর মাত্র দু’মাসের মধ্যেই সন্তানসম্ভবা হন, এবং ১৮৮১ সালে জন্মগ্রহণ করেন কীর্তিভূষণ। কালীভূষণ যে এই ব্যাপারটাকে দৈব অনুগ্রহ বলেই গণ্য করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। হরপার্বতীর প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রতীক হিসেবে তার পরের বছরই তিনি তাদের তৃতীয় নয়নে দুটি হিরে বসিয়ে দেন। হিরে দুটি সংগৃহীত হয়েছিল এক গুজরাটি বণিকের কাছ থেকে। গুজরাত থেকে প্রতি পাঁচ বছরে অন্তত একবার সে নাকি পূর্বভারতে মণিমুক্তা বিক্রি করতে আসত।
কীর্তিভূষণের বয়স যখন পাঁচ বছর, কালীভূষণের তখন মৃত্যু হয়। আকস্মিক মৃত্যু। তিনি প্রতিদিন গঙ্গাস্নান করতেন। চন্দননগরের ঘাটে স্নান করতে গিয়ে একদিন তিনি আর বাড়িতে ফেরেন না। হঠাৎ বন আসায় তিনি ভেসে গিয়েছিলেন, পাড়ে উঠে আসতে পারেননি। ঘটনার তিনদিন পর মাইল কয়েক উজানে তার মৃতদেহের সন্ধান মেলে।
বিমলভূষণের গল্প এই পর্যন্ত আসার পর অরুণ সান্যাল তাকে বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, “কীর্তিভূষণই তো আপনার ঠাকুর্দা, তাই না?”
“আজ্ঞে হ্যাঁ।” বিমলভূষণ বললেন, “আমার প্রপিতামহের তিনিই একমাত্র সন্তান। তার পরে আর আমার প্রপিতামহ কালীভূষণের অন্য কোনও পুত্রকন্যা হয়নি।”
“কালীভূষণও তো তার বাবার একমাত্র সন্তান?”
“আজ্ঞে হ্যাঁ।”
“কীর্তিভূষণকে তা হলে পাঁচ বছর বয়েস থেকে বড় করে তুললেন কে? আর ওই সম্পত্তি? মানে কালীভূষণের সম্পত্তিও তো নেহাত কম ছিল না। সে-সবের দেখাশুনোই
বা কে করতেন?”
“সবই করতেন আমার প্রপিতামহী, অর্থাৎ শান্তিলতা দেবী।” বিমলভূষণ বললেন, “অবিশ্যি নায়েব-গোমস্তারা ছিল না, তা নয়। দূর-সম্পর্কের কিছু পোষ্যও ছিল। কিন্তু আমার প্রপিতামহীর অনুমতি ছাড়া কারও কিছু করার সাধ্য ছিল না। তা সে অনুমতিই বলুন আর হুকুমই বলুন। ছেলেবেলায় আমার ঠাকুর্দার কাছে অন্তত সেইরকমই শুনেছি।”
“তার মানে তিনি খুবই কড়া ধাতের মহিলা ছিলেন, কেমন?”
“আজ্ঞে তা বলতে পারেন।”
সদানন্দবাবু বললেন, “ওই যাকে ছুঁদে মেয়েছেলে বলে আর কী।”
ভাদুড়িমশাই এতক্ষণ পর্যন্ত মাথা নিচু করে চুপচাপ সব শুনে যাচ্ছিলেন। একটাও কথা বলেননি। সদানন্দবাবুর মন্তব্য শুনে তিনি চকিতে একবার মুখ তুলে তার দিকে তাকালেন। যে-রকম ভুরু কুঁচকে তাকালেন, তাতে বুঝলুম, মন্তব্যটা তার পছন্দ হয়নি। ‘মেয়েছেলে’ শব্দটা তার কানে নিশ্চয় আপত্তিকর ঠেকে থাকবে।
তবে, যার প্রপিতামহী সম্পর্কে এই অশিষ্ট শব্দ প্রয়োগ, তার কোনও ভাবান্তর দেখলুম না। বরং সদানন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে সমর্থনসূচক ভঙ্গিতে উপর-নীচে একবার শির-সঞ্চালন করে তিনি বললেন, “একেবারে খাঁটি কথাটাই বলেছেন। আমার ঠাকুমা অবিশ্যি তার শাশুড়ির কথা উঠলে উঁদে না বলে বলতেন জাহাবাজ মেয়েছেলে। তারই কাছে শুনেছি যে, আমার ঠাকুর্দার লাইফকে তিনি একেবারে হেল করে ছেড়ে দিয়েছিলেন!”
“কী-রকম, কীরকম?” উৎসাহিত হয়ে সদানন্দবাবু তার শরীরটাকে একটু এগিয়ে এনেছিলেন। সেই অবস্থায় মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, “মায়ের পারমিশান না নিয়ে আপনার ঠাকুর্দার কিছু করার উপায় ছিল না বুঝি?”
“কিছু না।” বিমলভূষণ বললেন, “উঠতেও পারমিশান চাই, বসতেও পারমিশান চাই। মায়ের পারমিশান পাননি বলে নাকি জীবনে কখনও শ্বশুরবাড়িই যাওয়া হয়নি আমার ঠাকুর্দার। ঠাকুমার কাছে শুনেছি, তারও বাপের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন।”
“অ্যাঁ?” সদানন্দবাবু ডুকরে উঠে বললেন, “বাপের বাড়ি যাওয়া বন্ধ?”
“বিলকুল। এ কি ভাবা যায়?”
“না, ভাবা যায় না।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “কিন্তু ও-সব বাদ দিয়ে এবারে কাজের কথায় আসুন। আপনার সমস্যা তো দুটো হিরে নিয়ে। তাব কী হল? ও দুটো কি চুরি হয়ে গেছে?”
প্রসঙ্গ একেবারে হঠাৎই পালটে যাওয়ায় বিমলভূষণ সম্ভবত ফের একটু বিভ্রান্ত বোধ করছিলেন, সেটা কাটিয়ে উঠে বললেন, “ও হ্যাঁ, হিরে। না, চুবি হয়ে যায়নি। কিন্তু হবে।”
“জানলেন কী করে?”
“আমাদের পুজুরি ঠাকুর বলছিলেন, গঙ্গার ঘাটে দু’জন লোককে তিনি এই নিয়ে বলাবলি করতে শুনেছেন।
“এটা কবেকার কথা?”
“মাসখানেক আগের। তার হপ্তা দুয়েক বাদেই আমি বাঙ্গালোরে ফোন করি।”
শুনে একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন ভাদুড়িমশাই, তারপর বললেন, “হরপার্বতীর মূর্তিতে কি সারা বছরই হিরে দুটো পরানো থাকে?”
“আজ্ঞে না,” বিমলভূষণ বললেন, “পরানো হয় শুধু চৈত্রসংক্রান্তির দিনে।”
“কিন্তু তার তো আর দেরি নেই।”
“আজ্ঞে না। আজ এগারোই এপ্রিল, চোদ্দো তারিখে সংক্রান্তি। মাঝখানে আর মাত্তর দুটো দিন। হিরে দুটো সিন্দুকে ভোলা আছে। চোদ্দো তারিখের সূর্যোদয়ের আগেই সিন্দুক থেকে বার করে হরপার্বতাঁকে পরিয়ে দেব।”
শুনে, আবার একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন ভাদুড়িমশাই, তারপরে বললেন, “আপনি চন্দননগরে ফিরছেন কবে?”
“আজই ফিরে যাব।”
“ভাল। আমি কাল সকালে যাচ্ছি। আপনি ঠিকানাটা লিখে দিয়ে যান।”
বিমলভূষণ একটা ছাপানো কার্ড বার করে ভাদুড়িমশাইয়ের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, “ঠিকানা এতেই আছে। তবে কিনা দরকার হবে না। চন্নননগরে গিয়ে যে কাউকে আমার নাম বললেই রাস্তা দেখিয়ে দেবে।”
ভাদুড়িমশাইয়ের হাত থেকে নিজের ছড়িখানা ফেরত নিয়ে, নমস্কার করে ভদ্রলোক বেরিয়ে যাচ্ছিলেন। পেছন থেকে ভাদুড়িমশাই বললেন, “ও হ্যাঁ, একটা কথা ছিল।”
ঘুরে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক বললেন, “বলুন।”
“আপনি কলপ দেওয়া বন্ধ করলেন কেন?”
এতক্ষণে হাসলেন বিমলভূষণ। বললেন, “চামড়ায় একটা র্যাশ বেরোচ্ছিল। ডাক্তারের অ্যাডভাইসে বন্ধ করেছি।”
.
॥ ৩ ॥
বিমলভূষণকে লিফট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়েছিল কৌশিক। ফিরে এসে বলল, “বাবা রে বাবা! সোনা নয়, এপো নয়, হিরে! তাও আবার একটা নয়, একজোড়া! দাম কত হবে, মামাবাবু?”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “তা কী করে বলব? কত ক্যারাট, তা-ই তো জানি না। তবে হ্যাঁ, যদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল হিরে হয়তো খুববেশি দাম না-হওয়াই সম্ভব।“
আমি বললুম, “আপনি তা হলে কালই ওখানে যাচ্ছেন?”
“যাওয়াই উচিত।” অরুণ সান্যাল বললেন, “গাড়িতে করে গেলে চন্দননগরে পৌঁছতে কতক্ষণই বা লাগবে।”
কৌশিক বলল, “মেরেকেটে ঘণ্টা দেড়েক। অবিশ্যি যদি জি.টি. রোডে জ্যাম না থাকে। যা মামাবাবু, ঘুরেই এসো।
ভাদুড়িমশাই বললেন, “আর তুই এখানে বসে ছুটি কাটাবি আর মায়ের রান্না করা ভালমন্দ খাবি, কেমন?”
“ও কতা কইবেন না, ওকতা কইবেন না,” সদানন্দবাবু বললেন, “খাওয়ার কতাই যদি বলেন, তো আমি বলব, খাওয়ার জিনিস চন্নননগরেও কিছু কম নেই। সুজ্যি ময়রার জলভরা তালশাঁসের নাম শুনেছেন?”
অরুণ সান্যাল বললেন, “সেটা আবার কী বস্তু?”
“সন্দেশ। বাইরে ছানা, ভেতরে পিওর নলেন গুড়। অবিশ্যি এখন চত্তির মাস, নলেন গুড়ের টাইম নয়, তাই গুড়ের বদলে ক্ষীর দেবে। পাতলা ক্ষীর।”
“খেতে খুব ভাল?”
শুনে এমনভাবে সদানন্দবাবু অরুণ সান্যালের দিকে তাকালেন যে, তাতেই বোঝ গেল, এর চেয়ে হাস্যকর প্রশ্ন তিনি জীবনে কখনও শোনেননি। বললেন, “ভাল কী বলচেন মশাই, সে তো দেবভোগ্য জিনিস। একবার যদি খেয়েচেন তো বাদবাকি জীবন তার সোয়াদ আপনার মুকে লেগে থাকবে।”
“ওরেব্বাপ রে, কৌশিক হেসে বলল, “চন্দননগর বলতে আমাদের তো একদিকে যেমন দুপ্লের নাম মনে পড়ে, অন্যদিকে তেমনি মনে পড়ে বীর বিপ্লবী কানাইলাল দত্তের কথা। আপনি সেখানে মিষ্টির খবরও রাখেন দেখছি। এতসব ডিটেলস জানার সময় পান কোথায়?”
যেমনভাবে অরুণ সান্যালের দিকে তাকিয়েছিলেন, আস্তে আস্তে মুখ ঘুরিয়ে ঠিক তেমনিভাবেই এবারে কৌশিকের দিকে তাকালেন সদানন্দবাবু। তারপব বললেন, “ওহে ছোকরা, আমাকে দুপ্লে দেকিয়ো না। এই শ্যালদায় থাকি বটে, কিন্তু আসলে আমি কোতাকার লোক?”
ঘাবড়ে গিয়ে কৌশিক বলল, “কেন, তারকেশ্বরের।”
“অ্যান্ড হোয়্যার ইজ তারকেশ্বর?”
এইভাবে যে তার ভূগোল জ্ঞানের পরীক্ষা নেওয়া হবে, কৌশিক তা ভাবতে পারেনি। একটু থতমত খেয়ে মাথা চুলকে বলল, “হুগলি জেলায়। ভুল বললুম?”
“না না, ভুল বলবে কেন, সদানন্দবাবু বললেন, “কারেক্ট আনসার দিযেচ। দশে দশ। তবে কিনা, তারকেশ্বর জায়গাটা হুগলি জেলার মদ্যে হলেও উইদিন দি জুরিসডিকশন অব দি সাবডিভিশন অব চন্নননগর। আর সেদিক থেকে দেকতে গেলে আমি তো চন্নননগরেরই বাসিন্দে হে।”
অরুণ সান্যাল বললেন, “তা তো বটেই।”
সদানন্দবাবু বললেন, “তবেই বুজুন। তা আমি যদি না সেখেনকার হাডিৰ খপর রাকি, তো কে রাকবে। চনননগরের মিষ্টি তো ভালই, সেখেনকার গঙ্গাব তোপসে আর ইলিশও অতি চমৎকার।..আর হ্যাঁ, চাপাকলা থেকে যে ওয়াইন এখেনে সেব করে, তা তো কোনও তুলনাই হয় না।
ভাদুড়িমশাই বললেন, “খেয়ে দেখেছেন?”
“রামশ্চন্দ্র!” জিব কেটে সদানন্দবাবু বললেন, “বাপ-ঠাকুদ্দা খেতেন, তেনাদের কাছে নিচি। শুনে লোভ হয়েছিল বলে একবার এক বোতল ওই ওয়াইন জোগাড় করে বাড়িতে যে নিয়ে আসিনি, তাও নয়। কিন্তু আমার ওয়াইফকে তো চেনেন, রেশনের ব্যা; থেকে বোতলটা বার করতেই তিনি এমন হল্লা জুড়ে দিলেন যে, সে আর কহতব্য নয়।…না না, পয়সাটা স্রেফ জলে গেল, পয়সা দিয়ে যা কিনে আনলুম, তা আর আমার খাওয়া হয়নি।”
“বোতলটা কী হল? মিসেস বোস সেটা আছড়ে ভাঙলেন?”
“তা হলেও তো বুজতুম।” সদানন্দবাবু কাতর গলায় বললেন, “কিন্তু তাই-ই বা তিনি ভাঙলেন কোতায়। পরের দিন তার ছোট ভাই আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এয়েছিল। দিদির বাড়িতে এক থালা সন্দেশ রসগোলা সাঁটিয়ে যখন বিদেয় নিচ্ছে, তখন বোতলটা তার হাতে তুলে দিয়ে বললে, এটা নিয়ে যা, তোর জামাইবাবু তোরই জন্যে নিয়ে এয়েচে, খুব পষ্টিকর জিনিস।…একচোকোমি আর কাকে বলে।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “ও নিয়ে আব দুঃখ করবেন না বোসমশাই, আমার সঙ্গে চন্দননগরে যাচ্ছেন তো?”
“তা তো যেতেই হবে, তা নইলে ওখানকার রাস্তাঘাট আপনি চিনবেন কী করে? ও তো বলতে গেলে আমারই জায়গা।”
“ঠিক আছে, ওই চাপালার ওয়াইন তা হলে ওখানেই আপনাকে খাইয়ে দেবখন।” ভাদুড়িমশাই হাসতে হাসতে বললেন, “আমি অবশ্য ওই জন্যে চন্দননগরের কেসটা হাতে ‘নিইনি। সন্দেশ কিংবা তোপসে আর ইলিশের জন্যেও না।”
“তা হলে?”
“ওখানে আমার এক বন্ধু আছেন, অনেক দিনের পুরনো বন্ধু, কিন্তু অনেক কাল দেখা হয় না। বিমলভূষণের কাজটা নিতে যে এক কথায় রাজি হয়ে গেলুম, সেটা আসলে এই বন্ধুটির টানে।”
জিজ্ঞেস করলুম, “চন্দননগরে কি ওই বন্ধুর বাড়িতেই উঠবেন আপনি?”
“একা আমি কেন, আমরা তিনজনেই উঠব।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “তবে কোথায় উঠব, সেটা এখন বলা যাচ্ছে না। আগে তো চন্দননগরে যাই, বিমলভূষণের সঙ্গে কথা বলি, তারপর যদি দেখি যে, কাজের সুবিধের জন্যে শিবমন্দিরের কাছাকাছি থাকা দরকার, তো তাই বুঝে বিমলভূষণ যেখানে ব্যবস্থা করেন, সেখানেই থাকা যাবে।”
এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন ভাদুড়িমশাই। একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠিটাকে শূন্যে বার দুই-তিন ঝাঁকি মেরে, নিবিয়ে, অ্যাশট্রেতে ফেলে দিয়ে বললেন, “পরমেশের…আই মিন আমার এই চন্দননগরের বন্ধুটির..বাড়িটি ভারি সুন্দর। স্ট্যান্ডের খুব কাছেও বটে।…ওরে কৌশিক, তুই কখনও চন্দননগরে গেছিস?”
কৌশিক মাথা নাড়ল। “না, মামাবাবু।”
“পণ্ডিচেরিতে?”
এবারেও কৌশিককে দু’দিকে মাথা নাড়তে দেখে ভাদুড়িমশাই বললেন, “তাও না? তবে আর তুই জানবি কী করে যে, ওয়াটারফ্রন্টকে ফরাসিরা কত সুন্দরভাবে কাজে লাগায়। অন্তত এই একটা ব্যাপারে আমি তো ওদের কোনও তুলনাই খুঁজে পাই না।”
সদানন্দবাবু উশখুশ করতে শুরু করেছিলেন। গলা খাকরে বললেন, “একটা কতা জিগেস করব?”
“স্বচ্ছন্দে।”
“এই ওয়াটারফ্রন্ট জিনিসটা কী?”
প্রশ্ন শুনে কৌশিক হোহো করে হাসতে শুরু করেছিল। ভাদুড়িমশাই তার দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটা ধমক দিলেন। “বাঁদরামো করিস না।” তারপর মুখ ফিরিয়ে সদানন্দবাবুকে বললেন, “সমুদ্র, নদী কিংবা হ্রদের ধার। ওই মানে যেখানে যেটা পাওয়া যায় আর কি। তো সেটাকেই অতি সুন্দর করে ওরা সাজিয়ে তোলে।”
আমি বললুম, “কত সুন্দর করে, পণ্ডিচেরির সমুদ্রের ধারটা দেখলেই সেটা বোঝ যায়। বিকেলে গিয়ে বেড়াবার পক্ষে একেবারে আদর্শ জায়গা।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “চন্দননগরে গঙ্গার ধারে স্ট্যান্ডটাই কি কিছু কম সুন্দর? এখন অবশ্য একটা মন্দির বানিয়ে গঙ্গার ভিউটাকে এক জায়গায় একটু আটকে দিয়েছে। ওটা ওখানে না বানালেই পারত।”
“কই,” সদানন্দবাবু বললেন, “চন্নননগরে তো এককালে প্রায়ই যেতুম, বিশেষ করে সেখেনকার জগদ্ধাত্রী পুজোর সময়, কিন্তু স্ট্র্যান্ডে অমন মন্দির তো একবারও আমি দেকিনি।”
সদানন্দবাবুর কথা শুনে এতক্ষণ আমার মনে হচ্ছিল যে, চন্দননগর সম্পর্কে তিনি একজন অথরিটি, ওটা তাবই জায়গা, ওখানকাব যাবতীয় ব্যাপার তার নখদর্পণে। কিন্তু তার এই শেষ কথাটা শুনে মনে হল, দীর্ঘকাল তিনি ওদিকে যাননি। মনে হবার কারণ আর কিছুই নয়, বছর তিনেক আগে আমাকে একবার চন্দননগরে যেতে হয়েছিল, স্ট্র্যান্ডের মন্দিরটি তখন আমারও চোখে পড়েছে। অথচ সদানন্দবাবু ওটা দেখতেই পাননি?
ব্যাপারটা ভাদুড়িমশাইও ধরতে পেরেছিলেন। বললেন, “এককালে ওখানে প্রায়ই যেতেন বলছেন। তা এককাল মানে কতকাল আগে?”
সদানন্দবাবু একটুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, “অত তো হলপ করে বলতে পারব না, মশাই, সন-তারিখ সব ঠিকঠাক মনেও নেই। তবে লাস্ট কবে গেসলুম, সেটা বলতে পারি।”
“কবে?”
“সেই যে কলকাতায় জাপানি বোমা পড়ল, সেই বার। হাতিবাগান বাজারে বোমা পড়েছেল না?”
“ওরেব্বাবা, ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, “সে তো আর্লি ফর্টিজের ঘটনা। চন্দননগরে তখন পুরোদর ফরাসি শাসন চলছে। সে কি আজকের ব্যাপার?”
“তাতে কী হল?”
“কী আর হবে, স্ট্র্যান্ডের এই মন্দির তখন হয়ইনি। তা হলে আর আপনি দেখবেন কী করে?”
আমি বললুম, “চন্দননগর স্বাধীন হয়েছে বাদবাকি ইন্ডিয়ার পরে। আমরা স্বাধীন হলুম সাতচল্লিশে, আর এখানকার ফ্রেঞ্চ কলোনিগুলি স্বাধীন হল ফিফটিতে। স্বাধীন হল মানে ডি ফ্যাকটো ট্রান্সফার অব পাওয়ার হয়ে গেল। ফ্রান্সের ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লিতে সেটা পাস হতে অবিশ্যি আরও দু’দুটো বছর লেগে গেল। যা-ই হোক, এই মন্দির তারও অনেক পরের ঘটনা। গঙ্গার ভিউটা আটকে না দিয়ে ওটা অন্য কোথাও করলেই ভাল হত।
সদানন্দবাবু বললেন, “ফরাসিরা থাকলে ওটা এখেনে হতে পারত না বলচেন তো? ঠিক আছে, সেটা আমি মেনে নিচ্ছি। তবে কিনা গঙ্গার পাড়টা সুন্দর করে বাঁদিয়ে দিয়েছে বলেই যে সব ব্যাপারে তারা সায়েবদের চেয়ে ভাল ছিল, তা কিন্তু ভাববেন না।”
অরুণ সান্যাল বললেন, “সাহেবদের চেয়ে মানে? ফরাসিরা সাহেব নয়?”
“আহাহা, সদানন্দবাবু বললেন, “তা বলছি না, তা বলছি না, আসলে…ওই মানে….” বলে আর কথাটা শেষ করলেন না।
কৌশিক বলল, “বুঝেছি। বোস-জেঠু আসলে বলতে চান যে, ফরাসিরাও সাহেব বটে, তবে বোস-জেই যেখানে চাকরি করতেন, সেই জেনিস অ্যান্ড জেস্কিন কোম্পানির বড়সাহেবের মতো কুলীন-সাহেব নয়।”
“বটেই তো৷” সদানন্দবাবু একটু মিইয়ে গিয়েছিলেন, এবারে ফের তেড়ে উঠে বললেন, “ব্যাটারা ব্যাং খায়।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “শুধু ব্যাং কেন, খরগোশও খায়।”
“আহাহা, খরগোশের কতা হচ্ছে না। খাক না, যত খুশি খরগোশ খা। কিন্তু তাই বলে ব্যাং ও কি একটা খাবাব মতো জিনিস হল?”
“নয় কেন?” ভাদুড়িমশাই বললেন, “ফ্রান্সে থাকতে আমি প্রচুর ব্যাং খেয়েছি। খেতে যে খুব খারাপ, তাও বলতে পারছি না। কী বলব, ব্যাঙের ঠ্যাং অনেকটা মুরগির ঠ্যাঙের মতোই। তবে কিনা আরও সফ্ট।”
সদানন্দবাবু ফুঁসে উঠে বললেন, “আপনি খেতে পারেন, তবে ইংরেজরা খাবে না। কভি নেহি। খিদেয় মরে গেলেও খাবে না।”
ভাদুড়িমশাই হেসে বললো, “এই সেঞ্চৱিব গোড়ার দিকেও খাস লন্ডনের গলিতে গলিতে কী বিক্রি হত জানেন “
“কী বিককিরি হত?”
“আমাদের এখানে ফিরিওয়ালারা যেমন দুপুরের দিকে ঝাঁকা মাথায় গলিতে গলিতে হেঁকে বেড়ায় ‘ভেটকি মাছের কাটা চাই,’ ওখানে তেমনি ফিরিওয়ালারা হেঁকে বেড়াত ‘ক্যাট মিট’। হ্যাঁ, বেড়ালের মাংস।”
শুনে চোখ গোল হয়ে গেল অকণ সান্যালেরও। অবিশ্বাসের গলায় বললেন, “সত্যি?”
“ষোলো আনার উপরে আবও দু’আনা চড়িয়ে বলছি, আঠারো আনা সত্যি।“ ভাদুড়িমশাই বললেন, “ব্রিগস সাহেবের নাম শুনেছ?”
কৌশিক বলল, “তিনি আবার কে?”
“এস ব্রিগস। ইতিহাসের অধ্যাপক। অক্সফোর্ডে পড়াতেন। কথাটা তিনিই বলেছেন।”
“রামশ্চন্দ্র!” সদানন্দবাবু নাক কুঁচকে বললেন, “ইংরেজরা বেড়ালের মাংস খেত?”
ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, “আপনাদের কোম্পানির বড়সাহেব মিঃ জেঙ্কিনসের মতো পয়সাওয়ালা ইংরেজরা কেন খেতে যাবে। না না, তারা খেত না। তবে গরিব ইংরেজরা খেত।…আরে মশাই, না খেয়ে যাবে কোথায়? শীতের দেশ, শরীর গরম রাখার জন্যে মাংস তো খেতেই হবে, তা গোরু-ভেড়ার মাংস খাবার মতো রেস্তো যখন নেই, তখন বেড়াল না খেয়ে উপায় কী?”
অরুণ সান্যাল বললেন, “ওই যে কথা আছে না মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ, এ তো দেখছি তা-ই।”
“ঠিক তা-ই।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “কারে পড়লে মানুষ কী না খায়। সাপ, ব্যাং, ইঁদুর, বেড়াল, সবই তখন তার ভোজ্য। তবে হ্যাঁ, ফরাসিরা যে পয়সার অভাবে ব্যাং খায়, তা কিন্তু নয়। ওদের মেনুতে ওটা একটা ডেলিকেসি।”
“তার মানে বেশি পয়সা দিয়ে ওরা ওটা খায়?”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “বেশ আয়েস করে খায়।”
কথাটা আর এগোল না। কেন না, কাজের মেয়েটি এসে জানিয়ে দিল যে, আমাদের খেতে দেওয়া হয়েছে। সদানন্দবাবু সোফা ছেড়ে উঠতে-উঠতে বললেন, “যা সব আলোচনা হল, তাতে আর খেতে বসতে বিশেষ উৎসাহ পাচ্ছি না।”
.
॥ ৪ ॥
আজ বাবোই এপ্রিল, সোমবার। বেলা এখন বারোটা। কলকাতা থেকে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বওনা হয়েছিলুম, আধঘণ্টা আগে আমরা চন্দননগরে এসে পৌঁছেছি। আমবা মানে ভাদুড়িমশাই, সদানন্দবাবু, কৌশিক আর আমি। পরশু সংক্রান্তি। কৌশিক মাত্র একটা দিনের জন্য এসেছে, কালই কলকাতায় ফিরে যাবে, সংক্রান্তি পর্যন্ত থাকবে না।
আমরা উঠেছি পরমেশ চৌধুরির বাড়িতে। ইনি ভাদুড়িমশাইয়ের বন্ধু। কালই ভাদুড়িমশাইয়ের কাছে এঁর কথা শুনেছিলুম। বন্ধু বলে পৰিচয় দেওয়ায় ধরে নিয়েছিলাম যে, ইনি আমাদেরই বয়সী হবেন। তা কিন্তু নন। এর বয়স ষাট-বাষট্টিব বেশি হবে না। দেখে অন্তত সেইরকমই মনে হয়। ষাট-বাষট্টিতেও অনেকের শরীর অবশ্য ভেঙে যায়। এঁর ভাঙেনি। দোহারা চেহারার শক্তপোক্ত মানুষ। থুতনির নীচে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, মাথায় চকচকে টাক, মুখে সব সময়েই এক টুকরো হাসি লেগে আছে।
স্ট্যান্ডের ধারে এখানকার ট্রেজারি বিল্ডিংয়ের গা ঘেঁষে যে রাস্তাটি শহরে কেঁদের দিকে চলে গেছে, সেটা ধরে সামান্য কিছুক্ষণ হাঁটলেই পরমেশবাবুর বাড়িতে পৌঁছে যাওয়া যায়। ফ্রেঞ্চ কলোনিয়াল আর্কিটেকচারের উঁচু ভিতের ও উঁচু ছাতের একতলা বাড়ি, সামনের বারান্দাটি বেশ বড়সড়, ছাত থেকে কাঠের জাফরি ফুট কয়েক নেমে এসে বারান্দার উপরের অংশটিকে তিনদিকে ঘিরে বেখেছে।
ঢালাও বাড়ি, সংলগ্ন জমির আয়তনও নেহাত কম হবে না, তাতে ছোটবড় কিছু গাছপালা। তার মধ্যে, ছোট-ছোট নীল রঙের ফুল দেখে, বৃহৎ একটি জাকারান্ডা গাছকে খুব সহজেই চিনে নেওয়া গেল। শুনলুম, বাড়ির ছাত থেকে গঙ্গা দেখা যায়। এও জানা গেল যে, একজন ভৃত্য ও একটি পাঁচককে নিয়ে পরমেশ এখানে একা থাকেন। ভদ্রলোকের ছোটখাটো একটা ব্যবসা ছিল, বছর কয়েক আগে সেটা বিক্রি করে দিয়েছেন। টাকা-পয়সার অভাব যে নেই, সেটা ভাদুড়িমশাইয়ের কাছে শুনেছি। ব্যাঙ্কে জমানো টাকার থেকে যে সুদ মেলে, তারও একটা সামান্য অংশই খরচা করার দরকার হয়।
পরমেশবাবু নিঃসন্তান নন। দুটি ছেলে। বড়টি প্রবাসী, মার্কিন মুলুকে থাকে। ছোটটি থাকে দিল্লিতে। সেখানে সে একটি মালটিন্যাশনাল কোম্পানির রিজিওনাল ম্যানেজার। বিয়ে করেনি, মা’কে নিজের কাছে নিয়ে রেখেছে। বাপকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু পরমেশবাবু যাননি। তার কথা শুনে বোঝা গেল, চন্দননগরে থাকতেই তার ভাল লাগে, অন্য কোথাও তার মন টেকে না।
এর মধ্যে এমন দুটি ঘটনা ঘটেছে, যার এখানে উল্লেখ করা দরকার।
কাল দুপুরে বিমলভূষণ বিদায় নেবার পরেও বেশ কিছুক্ষণ আমাদের কথাবার্তা চলেছিল। তারপর আমাদের খাওয়ার ডাক পড়ে। খাওয়ার পর্ব শেষ হবার পরে ভাদুড়িমশাইয়ের খেয়াল হয় যে, তার সিগারেট ফুরিয়ে গেছে। কৌশিককে তিনি মোড়ের দোকান থেকে সিগারেট আনতে পাঠান। মিনিট কুড়ি-পঁচিশ বাদে কৌশিক ফিরে এসে বলে যে, বিমলভূষণকে সে ওই মোড়ের কাছেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে তিনি কথা বলছিলেন। ভদ্রলোক বিদেশি। কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল একটা পুরনো সিট্রোয়েন গাড়ি। কথা শেষ করে বিদেশি ভদ্রলোকটি সেই গাড়িতে উঠে পড়েন। “আর বিমলভূষণ?” ভাদুড়িমশাইয়ের এই প্রশ্নের উত্তরে কৌশিক জানায় যে, তিনি রাস্তা পেরিয়ে উল্টো দিকের ফুটপাথে ওঠেন। তারপরে আর আমি তাকে দেখতে পাইনি। বিদেশি মানুষটি ঠিক কোন দেশের মানুষ, তা সে বুঝতে পেরেছে কিনা, তাও জিজ্ঞেস করেছিলেন ভাদুড়িমশাই। কৌশিক তাতে বলে যে, তা সে বুঝে উঠতে পারেনি। সে শুধু এইটুকুই বলতে পারে যে, ভদ্রলোকের পরনে ছিল জলপাই রঙের প্যান্ট আর সাদা শার্ট। তা ছাড়া তাঁর বাঁ গালে একটা কাটা দাগও তার চোখে পড়েছে। হাইট মাঝারি, চুলের রং নুন মেশানো গোলমরিচের মতন, চোখের তারা নীল। এ ছাড়া আর কিছু তার চোখে পড়েনি।
এটি তো প্রথম ঘটনা। দ্বিতীয় ঘটনাটি আজ ঘটেছে। শ্রীরামপুরের রাস্তায় একটু জ্যাম ছিল। সেটা ছাড়িয়ে, চা খাওয়ার জন্যে আমরা রাস্তার ধারের একটা বাবার সামনে গাড়ি থামাই। ভাদুড়িমশাই কৌশিককে বলেন, “আমরা আর গাড়ি থেকে নামব না। তুই ভিতরে গিয়ে চার কাপ চায়ের অর্ডার দে। চা যেন গাড়িতেই দিয়ে যায়। কৌশিক কিন্তু ধাবার ভিতরে ঢোকে না। খানিকটা এগিয়ে গিয়েও আচমকা ফিরে এসে, গলার স্বর নামিয়ে বলে, “সেই লোক। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ধাবা থেকে যে লোকটি বেরিয়ে আসে, তার বাঁ গালের কাটা দাগটা দেখেই আমি বুঝতে পারি যে, সেই লোক’ বলতে কৌশিক কার কথা বোঝাচ্ছিল। বাঁ কানের গোড়া থেকে দাগটা তার ঠোঁটের বা কোণ পর্যন্ত নেমে এসেছে। মিলে যাচ্ছে আরও কিছু বর্ণনাও। তবে এর প্যান্টটা আজ হালকা ধূসর রঙের, শার্টটা লাল, চেক কাটা। পোশাকের বং যে মিলছে না, সেটা বিচিত্র নয়, মানুষ নিশ্চয় রোজ-রোজ একই শার্ট-প্যান্ট পরে না। তা না-ই পরুক, একেবারে হঠাৎই আমার মনে হতে লাগল যে, আর-একটা ব্যাপারেও যেন একটা বড় রকমের অমিল থেকে যাচ্ছে। কিন্তু সেটা যে কোন ব্যাপারে, তক্ষুনি সেটা বুঝে উঠতে পারলুম না!
ভাদুড়িমশাই স্টিয়ারিং হুইলে হাত রেখে বসে ছিলেন। লোকটি এগিয়ে এসে সামনে ঈষৎ ঝুঁকে পড়ে ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে তাকে জিজ্ঞেস এল, “চন্দননগরে যেতে হলে কি এখান থেকেই ডাইনে গাড়ি ঘোরাব?”
“না,” ভাদুড়িমশাই বললেন, “এখানে নয়। আরও খানিকটা সিধে গেলে একটা চৌরাস্তার মোড় পাবেন, সেখান থেকে ডান দিকের রাস্তা ধরতে হবে।…বাই দ্য ওয়ে, আপনি কি এদিককার রাস্তাঘাট ভাল চেনেন না?”
“না, আমার নাম মাতা লুমিয়ের, আমি মাত্র তিনদিন হল ফ্রান্স থেকে এসেছি, এখানকার রাস্তাঘাট সম্পর্কে কোনও ধারণাই আমার নেই। একটা রোড ম্যাপ পেলে ভাল হত।”
“দরকার হবে না।” ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, “প্রায় তো পৌঁছেই গেছেন, বাকি পথটুকুও ঠিকই চলে যেতে পারবেন।
লোকটি আর কথা বাড়াল না। আমাদের ধন্যবাদ দিযে পথের ধারের একটা গাছতলায় দাঁড় করানো তার গাড়িতে গিয়ে উঠল। কৌশিক একটা পুরনো সিট্রোয়েন গাড়ির কথা বলেছিল। কিন্তু লক্ষ করলুম, এটা পুবনো গাড়ি তো নয়ই, সিট্রোয়েনও নয়, নতুন মডেলের ঝকঝকে একটা মারুতি এস্টিম।
লোকটি চলে যাবার পর কৌশিক বলল, “মামাবাবু, এই সেই লোক। রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিমলভূষণ কাল এরই সঙ্গে কথা বলছিলেন।”
“বুঝেছি।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “কিন্তু তুই এবারে গিয়ে চায়ের ব্যবস্থা করতো। অনেকক্ষণ চা খাইনি।”
ভাদুড়িমশাইয়ের কথা শুনে মনে হল, মাতা লুমিয়েরের সঙ্গে এই হঠাৎ সাক্ষাৎকার নিয়ে তিনি কিছুই ভাবছেন না।
যেন ধরে নিয়েছেন যে, এ খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।
আমার ধারণা কিন্তু অন্যরকম। আমার বিশ্বাস, লোকটি মোটামুটি আঁচ করে রেখেছিল, যে, এই সময়ে এই পথ দিয়ে আমরা চন্দননগবে যাব। বিমলভূষণের কাছে ও আমাদের কথা শুনেছে। কেন আমরা চন্দননগরে যাচ্ছি, তাও ও জানে। এখানকার রাস্তাঘাট ওর অচেনা নয়। মোটেই ও ফ্রান্স থেকে সদ্য এ-দেশে আসেনি। যার কান থেকে ঠোঁট পর্যন্ত অমন একটা কাটা দাগ থাকে, সে মোটেই সুবিধের লোক হতে পাবে না। পথের হদিশ জিজ্ঞেস করাটা ওর একটা ছল মাত্র। এইভাবে ও আমাদের একটু বাজিয়ে দেখে নিল। লোকটিকে দেখামাত্র আমার মনে একটা অস্বস্তি জেগেছিল। সেটা এখনও যায়নি। খালি খালি মনে হচ্ছে, এর সঙ্গে আবার আমাদের দেখা হবে। এবং সেই দেখাটা খুব প্রীতিকর হবে না।
কথা বলতে বলতে একটু পিছিয়ে গিয়েছি, এখন আবার এগিয়ে আসা যাক। মার্তা লুমিয়েরকে যেমন আমার একটুও ভাল লাগেনি, মনে হয়েছে যে, এ খুবই বিপজ্জনক মানুষ, তেমনি আবার পরমেশ চৌধুরিকে আমার প্রথম থেকেই বেশ ভাল লেগে গিয়েছে। কথা শোনার দরকার হয় না, দেখলেই বোঝা যায় যে, ইনি স্বচ্ছ মনের মানুষ, এঁর মধ্যে কোনও পাঁচঘোচের ব্যাপার নেই। ভাদুড়িমশাইয়ের কাছে আগেই শুনেছিলাম যে, পরমেশ চৌধুরির সঙ্গে তার সম্পর্ক নেহাত এক-আধ বছবের নয়, অনেক দিনের। এখন এদের কথাবার্তা শুনে বোঝা গেল, সম্পর্কটা বেশ গভীরও বটে। পরমেশ বলছিলেন যে, চন্দননগর ছাড়া অন্য কোথাও তার মন টেকে না।
শুনে ভাদুড়িমশাই বললেন, “কিন্তু এখানে তো তুমি একলা থাকো। অসুখ-বিসুখ হলে দেখবে কে?”
“সে তো তোমার সম্পর্কেও বলা যায়, চারুদা।” পরমেশ হেসে বললেন, “বউদি কবেই স্বর্গে গেছেন। একটি মাত্র মেয়ে, সেও বিদেশে থাকে। এখন বলো, অসুখ-বিসুখ তো তোমারও হতে পারে, তখন তোমাকেই বা কে দেখবে।”
“কেন, মালতী দেখবে।”
“কিন্তু মালতী তো কলকাতায় থাকে, আর তুমি থাকো বাঙ্গালোরে। হঠাৎ যদি তোমার কঠিন একটা অসুখ হয়? নাকি সেটা হতেই পারে না?”
ভাদুড়িমশাই হোহো করে হেসে উঠলেন। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, “কথাটা নেহাত মন্দ বলোনি হে। সত্যি এক-এক সময় মনে হয় যে, যমরাজের সঙ্গে একটা চুক্তি করেছি, জগিং করতে করতে হঠাৎ একদিন পটাং করে মরে যাব, তার আগে কোনও অসুখ বিসুখ আমাকে ছুঁতে পারবে না।”
এনে সদানন্দবাবু হা-হাঁ করে উঠলেন। “অমন কতা বলবেন না, অমন কতা বলবেন না। ও সব নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা করতে নেই। অসুক তো হতেই পারে।”
“তা যদি হয়ই, তো কৌশিক রয়েছে কী করতে?” ভাদুড়িমশাই বললেন, “অসুখ হলে যাতে এই বুড়ো বয়েসে একটু সেবাযত্ন পাই, তারই জন্যে তো কৌশিককে বাঙ্গালোরে আমার কাছে নিয়ে রেখেছি।”
কৌশিক বলল, “বাজে বোকো না তো। জ্বর হলে যে মাথায় জলপট্টি দেওয়ার কাজটাও আমার দ্বারা হবে না, সে তুমি খুব ভালই জানো।”
ভাদুড়িমশাই পরমেশের দিকে তাকিয়ে বললেন, “ওর কথায় কান দিয়ো না, পরমেশ। সত্যিই যদি আমার কিছু হয়, তো কৌশিক তার মামাবাবুর জন্যে জান লড়িয়ে দেবে।….কিন্তু তুমি তোমাকে কে দেখবে? তোমার তো একটা ভাগ্নে পর্যন্ত এখানে নেই। তা হলে?”
পরমেশ হেসে বললেন, “তা হলে আমাকে কী করতে বলো?”
“দিল্লি চলে যাও। সেখানে তোমার বাদবাকি জীবনটা ছোট ছেলের কাছে থাকো।”
“দিল্লি গিয়ে আমি করবটা কী?”
“কেন, এই বয়েসে যা করা উচিত তা-ই করবে। সকালে ঘণ্টাখানেক হাঁটবে, খবরের কাগজ পড়বে, দুপুরে খাওয়ার পরে ঘণ্টা দুয়েক দিবানিদ্রা দেবে, তারপরে বিকেলে চা খেয়ে চিত্তরঞ্জন পার্কের কালীবাড়িতে গিয়ে বসে থাকবে।…কালীবাড়িটা দেখেছ?”
“চমৎকার জায়গা। টিলার উপরে পাশাপাশি তিনটি মন্দির। কালী, শিব আর রাধামাধবের। সামনে সবুজ ঘাসের লন। অতি সুন্দর পরিবেশ। চলে যাও হে পরমেশ, চলে যাও।”
“আর এই বাড়ি?” পরমেশ প্রায় আঁতকে উঠে বললেন, “এই বাড়ির কী হবে?”
“বিক্রি করে দেবে।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “যেমন ভিন্টেজ কার, তেমনি ভিন্টেজ বাড়িরও আজকাল খুব কদর। খদ্দেরের অভাব হবে না।”
শুনে হাঁ করে খানিকক্ষণ ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন পরমেশ চৌধুরি। তারপর সামনের দিকে আঙুল তুলে বললেন, “ওই গাছটা দেখছ?”
“দেখছি। ওটা জাকারান্ডা গাছ। কলকাতায় বিডন স্কোয়ারের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা আছে। আর একটা দেখেছি ভি. আই. পি. রোডের ধারে। দিল্লিতে হেলি রোডে বঙ্গভবনের কাছেও একটা দেখেছি। ওটা দক্ষিণ আফ্রিকার গাছ।…গুঁড়ি দেখে মনে হচে, বয়েস নেহাত কম হল না।”
‘নব্বুই চলছে।” পরমেশ বললেন, “শুধু দক্ষিণ আফ্রিকায় কেন, আফ্রিকার আরও কয়েকটা জায়গায় হয়। যেমন ধরো মিড়ল কঙ্গোয়। এককালে যেটা ছিল ফ্রেঞ্চ কলোনি। তো আমার ঠাকুর্দা তো এখানকার ফরাসি সরকারের কাজ করতেন। তার ওপরওয়ালা কঙ্গো থেকে এখানে বদলি হয়ে আসার সময় সঙ্গে করে কারান্ডার গুটিকয়েক চারা নিয়ে। এসেছিলেন। তার থেকে একটা তিনি ঠাকুর্দাকে দেন। অন্যগুলো বেঁচেছিল কি না জানি না, তবে এটা দিব্যি বেঁচে আছে।”
আমি বললুম, “কঙ্গো তো ছিল বেলজিয়ানদেব দখলে।
ভাদুড়িমশাই বললেন, “সবটা নয়। খানিকটাতে ফরাসি শাসন চলত। মিডল কঙ্গো, গ্যাবন আর উবাঙ্গি শারি–এই তিনটে জায়গা নিয়ে যে এলাকা, তাকে বলা হত ফ্রেঞ্চ ইকুয়েটরিয়াল আফ্রিকা।…তো পরমেশ, এই বাড়িটা তো আরও পুরনো। কত হল এর বয়েস?”
“তা অন্তত শ দেড়েক বছর।” পরমেশ বললেন, “এক ফরাসি সাহেব তাঁর নিজের জন্যে বানিয়েছিলেন। তার কাছ থেকে আমব ঠাকুর্দা যখন কেনেন, শুনেছি তখনই এই বাড়ির বয়েস নাকি পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে।“
একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন পরমেশ চৌধুরি। তারপর বললেন, “হুট করে এই বাডি কি বেচে দেওয়া যায়? এর সঙ্গে কত স্মৃতি জড়িয়ে বয়েছে। আমার ঠাকুর্দা আর ঠাকুমার স্মৃতি, আমার বাবা আর মায়ের স্মৃতি, আমার নিজের গোটা জীবনের স্মৃতি। জাকারান্ডা গাছটা তো আমার ঠাকুর্দার লাগানো। বাড়ির পিছনে একটি মস্ত ছাতিম গাছ রয়েছে, সেটা লাগিয়েছিলেন আমার বাবা। আর সামনের গেটের দু’পারে যে দুটি গোলমাথা বকুল গাছ দেখছ, এই দুটিই আমার মা লাগিয়েছিলেন। গাছগুলি দেখি, আর তাদের কথা মনে পড়ে। এ সব ছেড়ে আমি যাব কোথায়? আর তা ছাড়া, এই বাড়ি আর এই গাছপালার কথা যদি ছেড়েও দিই, এত চেনা লোকজনই বা কোথায় পাব? বলতে গেলে এখানকার প্রায় প্রত্যেকটি লোককে আমি চিনি।”
হঠাৎই একেবারে সরাসরি পরমেশের দিকে তাকালেন ভাদুড়িমশাই। তারপর বললেন, “বিমলভূষণ সেনকে চেনো?”
মনে হল পরমেশ একটু হকচকিয়ে গেছে। ভুরু কুঁচকে বললেন, “কোন বিমলভূষণ? মন্দিরবাড়ির?”
“হ্যাঁ। যে মন্দিরে হরপার্বতীর মূর্তি রয়েছে। দু’জনেরই থার্ড আই নাকি হিরের। সত্যি?”
“সত্যি।” পরমেশ বললেন, “শুনেছি বিমলভূষণের গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার ওই হিরেজোড়া নাকি এক গুজরাটি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিনেছিলেন। কিন্তু হরসূন্দরবাবু সেকথা বিশ্বাস করেন না।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “কে হরসুন্দরবাবু?”
“হরসুন্দর মুখুটি। বয়েস বিরানব্বই। বলতে গেলে এই চন্নননগরের গেজেট।” পরমেশ বললেন, “তার কাছে পাবে না, এমন খবর নেই।”
ভাদুড়িমশাইয়ের চোখ দেখলুম সরু হয়ে এসেছে। বললেন, “ভদ্রলোকের সঙ্গে একবার দেখা করা যায়?”
“বিলক্ষণ। তবে তিনি এখানে থাকেন না।”
“তা হলে কোথায় থাকেন?”
“দূরে নয়,” পরমেশ চৌধুরি হাত তুলে আশ্বাস দিয়ে বললেন, “খুবই কাছে। গড় পেরিয়ে ভদ্রেশ্বরে ঢুকে খানিক এগিয়ে ডাইনে একটা গলি। গলি ধরে এই ধরো মিনিট দুই-তিন হাঁটতে হবে, বাস।”
সদানন্দবাবু বললেন, “হাঁটতে হবে কেন?”
পরমেশ বললেন, “সরু গলি, গাড়ি ঢুকবে না। কী চারুদা, যাবে?”
“যাব তো অবশ্যই।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “কিন্তু কখন যাব।”
“যাওয়া তো এখুনি যায়।” পরমেশ বললেন, “কিন্তু আমি বলি কী, এই ভরদুপুরে গিয়ে কাজ নেই। বুড়ো এই সময়ে একটু জিরিয়ে নেয়। তা সেও জিরোক, তোমরাও খেয়েদেয়ে একটু জিরিয়ে নাও, তারপর এই ধরো চারটে নাগাদ বেরিয়ে পড়া যাবে। রাজি?”
“রাজি।”
.
॥ ৫ ॥
বিকেল চারটেতেই বেরিয়ে পড়া গেল। মারুতি এইট হান্ড্রেডের পিছনের সিটে তিনজন বসলে বড্ড ঠেলাঠেসি করে বসতে হয়, কিন্তু উপায় কী, আমি সদানন্দবাবু আর কৌশিক তা-ই বসলুম। সামনে স্টিয়ারিং হুইলের সামনে ভাদুড়িমশাই, তার পাশের আসনে পরমেশ চৌধুরি।
দুর্গ থাকলে তাকে ঘিরে একটা পরিখা থাকবে, এ খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু যেমন কলকাতার ক্ষেত্রে, তেমনি চন্দননগরের ক্ষেত্রেও গোটা শহর একটা পরিখা দিয়ে ঘেরা। কলকাতাকে গড়খাই দিয়ে ঘেরা হয়েছিল বাইরের শত্রুদের মূলত বর্গিদস্যুদের— হানাদারি ঠেকাবার জন্য। মারাঠা ডিচ নামটাই তার প্রমাণ। চন্দননগরের এই গড়খাইয়ের বয়েসও নেহাত কম হল না। পরে নানা সময়ে এর সংস্কার হয়ে থাকতে পারে, তবে এটি প্রথম কাটা হয়েছিল নাকি ১৬৭৬ সালে। শহরের তিনশো বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত একটি স্মারক পুস্তিকায় অন্তত এইরকমই দেখছি।
যা-ই হোক, গড়খাই পেরিয়ে আরও খানিকটা গিয়ে বড়রাস্তার ধারে আমাদের গাড়ি পার্ক করা হল। পরমেশ বললেন, “এবারে আমরা ডানদিকের গলিতে ঢুকব। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলে রাখি, চারুদা।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “তুমি কিছু বলার আগে বরং আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করব।”
“বেশ ভো, করো।”
“ভদ্রলোকের বয়েস তো শুনলুম বিরানব্বই। বাড়িয়ে বলোনি তো?”
“আরে না, পরমেশ চৌধুরি হেসে বললেন, “দু’বছর আগে ওঁর নব্বই বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরাই স্ট্র্যান্ড ওয়াকার্স অ্যাসোসিয়েশন থেকে ওঁকে একটা সম্বর্ধনা দিয়েছিলুম। আগে দু’বেলা স্ট্র্যান্ডে গিয়ে হাঁটতেন, এখন শুধু সকালে হাঁটেন।”
“তা হাঁটুন, কিন্তু অন্য সব ফ্যাকাল্টি ঠিক আছে তো?”
“তার মানে?”
“তার মানে চোখে ঠিকমতো দেখতে পান কি না, কানে ঠিকমতো শুনতে পান কি না, মেমারি ঠিকমতো কাজ করছে কি না, এই আর কি।”
সদানন্দবাবু মুরুব্বির চালে বলেন, “এই বয়েসে অনেকেরই ও-সব গুবলেট হয়ে যায় তো! তবে হ্যাঁ, আমার মনে হয়, এনার বেলায় তা হয়নি, সব ঠিক আছে।”
পরমেশবাবুর সঙ্গে কথা বলছিলেন ভাদুড়িমশাই। তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সদানন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন, “আপনি কী করে জানলেন? চেনেন নাকি?”
কোঁচকানো ভুরু দেখেই সদানন্দবাবু সম্ভবত একটু অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করেছিলেন। আমতা-আমতা করে বললেন, “না…মানে ঠিক যে চিনি তা নয়। তবে কিনা…ওই মানে…।”
“ওই মানে কী?”
“ওই মানে ভাবছিলুম যে, মর্নিং ওয়াক করেন তো, তাই নিশ্চয় শরীরের কলকজাগুলো বিগড়ে যায়নি।”
“বাস,” ভাদুড়িমশাই বললেন, “তাই থেকেই আপনি বুঝে গেলেন যে, লোকটার ফ্যাকালটিগুলো সব ঠিক আছে? ধন্যি লোক আপনি!”
ভাদুড়িমশাই আরও দু’একটা কথা বলতেন হয়তো, কিন্তু পরমেশবাবু তাকে বাধা দিয়ে বললেন, “না চারুদা, উনি ঠিকই বলেছেন। হরসুন্দরবাবু কানেও ঠিকই শুনতে পান, চোখেও ঠিকই দেখতে পান। আর হ্যাঁ, মেমারির কথা বলছিলে তো, হি হ্যাঁজ এ ফোটোগ্রাফিক মেমারি। জগদ্ধাত্রী পুজোর বিসর্জনের দিন কবে কোন ঠাকুরের হাইট নিয়ে গণ্ডগোল বেধেছিল, সেটা কোন ক্লাবের ঠাকুর, শেষ পর্যন্ত গণ্ডগোল কীভাবে মেটানো হয়, সব একেবারে গড়গড় করে বলে দেবেন। কিছু ভোলননি। রিমার্কেল স্মৃতি। তবে সেটা মর্নিং ওয়াকের জন্য হয়েছে কি না, তা বলতে পারব না।”
“বাঃ, তবে তো ভালই হল!” ভাদুড়িমশাই বললেন, “তা হলে আর দেরি করা কেন। চলো, এগোনো যাক।”
স্যাঁতাপড়া এঁদো গলি, বাড়িগুলির বেশির ভাগই একতলা, বাইরের দেওয়ালের পলেস্তারা খসে পড়েছে, ইটগুলো দাঁত বার করে আছে, এ-সব বাড়ির কোনওটারই বয়েস নেহাত কম হবে না। খানিকটা এগোনোর পর তারই একটার সামনে দাঁড়িয়ে পরমেশ বললেন, “এই বাড়ি। হুটোপাটির শব্দ শুনে মনে হচ্ছে, হরসুন্দরকাকা আবার কাউকে নিয়ে পড়েছেন।”
কাকে নিয়ে পড়েছেন, ভেজানো সদর দরজা ঠেলে ভিতরের উঠোনে ঢুকেই সেটা বোঝা গেল। মাথায় ঝাঁকড়া-চুলওয়ালা বছর ছয়-সাতের উদোম একটা রোগা ডিগডিগে ছেলে উঠোনের মাঝখানকার তুলসী-মঞ্চ ঘিরে দু’হাতে নিজের লজ্জাস্থান ঢেকে পরিত্রাহি চেঁচাতে চেঁচাতে দৌড়চ্ছে, আব হাতে একটা কাচি নিয়ে তার পেছাপেছন দৌড়চ্ছেন এক বৃদ্ধ। কাণ্ড দেখে আমরা যে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিলাম, সেটা স্বীকার করাই ভাল। পরমেশ চৌধুরির কথা আলাদা, তিনি সম্ভবত এই ধরনের দৃশ্য মাঝে-মাঝেই দেখে থাকেন, কিন্তু আমরা কেউই এর জন্যে ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না। উলঙ্গ অবস্থায় বাইরের লোজনদের সামনে পড়ে গিয়ে বাচ্চা ছেলেটিও নিশ্চয় এক মুহূর্তের জন্য ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। সেটা কাটিয়ে ওঠার আগেই বুড়ো মানুষটি খপ করে তার একটা হাত ধরে ফেলে হাঁক পাড়লেন, “রোঘা!”
হাঁক শুনে যাই দাদু’ বলে যে ছোকরা মতন ছেলেটি ভিতর বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে এল, তার বয়েস বছর উনিশ-কুড়ির বেশি হবে না। বেরিয়েই আমাদের দেখে সে অবাক। তারপর পরমেশবাবুর ওপর চোখ পড়তে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, “ও দাদু, পরমেশ জ্যাঠামশাই এসেছে।”
বৃদ্ধ যে তাই এনে বাচ্চা ছেলেটিকে ছেড়ে দিলেন, তা নয়। যে-ভাবে তার হাতটাকে ধরে রেখেছিলেন, সেইভাবে ধরে বেখে, আমাদের দিকে চোখ না ফিরিয়েই বললেন, “ওহে পরমেশ, দেখতেই পাচ্ছ যে, আমি এই বাদবটাকে নিয়ে ব্যস্ত আছি। তুমি বরং বাইরের ঘরে বসে একটু অপেক্ষা করো, আমি আমার হাতের কাজটা সেবে নিই, তারপর তোমার সঙ্গে কথা বলব অখন।”
বোঘে, যার নাম সম্ভবত রঘুনাথ কি রঘুবীর, আমাদের যে ঘরটিতে নিয়ে বসাল, তার একদিকে সূক্তনি-ঢাকা একটি তক্তপোশ, অন্যদিকে খান দুয়েক টিনের চেয়ার। আমাদের বসিয়ে মাথার উপরের ফ্যান চালিয়ে দিয়ে রোঘো বলল, “আপনারা একটু বসুন, দাদু এক্ষুনি এসে পড়বেন।”
পরমেশ বললেন, “ওটি কার ছেলে? মনুর?”
“না, না,” বোঘঘা হেসে বলল, “দাদার নয়। আসলে এই বাড়িরই নয়। এটি আমাদের পাশেরও পাশের বাড়ির। দত্তবাড়ির হারুদাকে চেনেন তো? ওই যে হেভি অ্যাকটিং করে? তার ছোট ছেলে।”
রোঘো বিদায় নিল। যাবার আগে বলে গেল, “আপনারা বসুন, আমি চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।”
চা আসার আগেই হরসুন্দর মুখুটি ঘরে এসে ঢুকলেন। বললেন, “পুরো এক হপ্তা ধরে তক্কেতক্কে ছিলুম, কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছিলুম না। বাঁদরটা আমাকে দেখতে পেলেই ছিটকে পালাত। কিন্তু আমসত্ত্বের লোভ আছে না? মনুর বউয়ের কাছে আমসত্ত্ব চাইতে বোজ এই বাড়িতে আসে তো। বাস, আজ আসতেই কাঁক করে চেপে ধরেছি।”
পরমেশ বললেন, “চুল কেটে দিয়েছেন তো?”
“তা আর বলতে! একেবারে উঁদি ঘেঁষে হেঁটে দিয়েছি। বুঝলে হে পরমেশ…” কথাটা শেষ করলেন না। একেবারে হঠাৎই আমাদের দিকে চোখ পড়ল হরসুন্দর মুখুটির। বললেন, “এরা কারা?”
“কলকাতার লোক। আমার বন্ধু। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।”
“আমার সঙ্গে?” হরসুন্দর বললেন, “কেন?”
“সেনেদের হরপার্বতীর হিরের চোখ নিয়ে কথা বলতে চান।”
বছর পনবো-ষোলোর একটি শ্যামলা রোগা মেয়ে মস্ত একটা কঁসার থালার উপরে ছকাপ চা আর একটা প্লেটে কিছু বিস্কুট সাজিয়ে নিয়ে ঘরে ঢুকে তক্তপোশেরই একদিকে থালাটা রেখে নিঃশব্দে আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। হরসুন্দর বললেন, “আগে চা খান, পরে কথা হবে।”
আমি আর সদানন্দবাবু সাধারণত দুধচিনি মেশানে! চা খাই না। এক্ষেত্রে মুখ বুজে খেয়ে নিলুম। দুধটা সম্ভবত ঠাণ্ডা ছিল, ফলে চাটাও একটু ঠাণ্ডা মেরে গেছে, খেতে তাই বিশেষ সময়ও লাগল না। চটপট চা খেয়ে যে-যার পেয়ালা থালায় নামিয়ে রাখলুম। হরসুন্দর মুখুটি কিন্তু সেই ঠাণ্ডা চাই বেশ সময় নিয়ে তারিয়ে তারিয়ে গেলেন। তারপর তিনিও তার পেয়ালাটিকে থালায় নামিয়ে রেখে বললেন, “আপনারা ঠিক কী জানতে চান বলুন দিকি।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “দামের কথাটা জানতে চাই।”
শুনে যেন ভারি অবাক হয়ে গেছেন এইভাবে হরসুন্দর খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে। তারপর বললেন, “কীসের দাম?”
পরমেশ বললেন, “সে কী হরসুন্দরকাকা, সেনেদের হরপার্বতীর থার্ড আইতে হিরে পরানো আছে না?”
“তা আছে বই কী।” হবসূদর বললেন, “তবে সম্বচ্ছর পরানো থাকে না, ওই শুধু চোত সংক্রান্তির দিনে পবিয়ে পরদিনই আবার খুলে নেওয়া হয়। কেন, তাতে হয়েছেটা কী?”
“খেলে যা!” পরমেশবাবু নিচু গলায় বললেন, “বুড়ো দেখছি ব্যাপারটা ঠিক ধরতেই পারছে না!”
কিন্তু, যত নিচু গলাতেই বলা হোক না কেন, হসূদবের কানে দেখলুম কথাটা ঠিকই পৌঁছে গেছে। শুনে রেগে যাওয়াটা স্বাভাবিক হত। কিন্তু তিনি রেগে গেলেন না, হেসে, একটা চোখ একটু ছোট করে বললেন, “তা হলে আর এই বুড়োর কাছে এসেছ কেন? ওই বিমলভূষণের কাছেই যাও, জোড়া হিরে নিয়ে ওর বাপ-ঠাকুর্দা যা বলত, আর ও নিজেও শুনি যা বলে বেড়াচ্ছে, সেই গপ্পোটাই শোনো গিয়ে।”
উত্তরে পরমেশ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ভাদুড়িমশাই তাকে বলতে দিলেন না। হাতের ইঙ্গিতে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, “গপ্পা কি না জানি না, তবে বিমলভূষণের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। হিরের ব্যাপারে তাঁর যে বক্তব্য, তাও শুনেছি। শুনে বিশ্বাসও করিনি, অবিশ্বাসও করিনি। পুরোপুরি বিশ্বাসই যদি করব, তবে সেটা আবার আপনার কাছে যাচাই করতে আসব কেন?”
কথাটা শুনে স্পষ্টতই খুশি হলেন হরসুন্দর মুখুটি। বললেন, “এসে ভাল করেছেন। এ ব্যাপারে আমি যা জানি, তা আপনাকে বলব বই কী, নিশ্চয় বলব। কিন্তু তার আগে শুনতে চাই যে, বিমল কী বলেছে। বলেনি যে, এক গুজরাটি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ওর ঠাকুর্দার বাপ ওটা কিনেছিল?”
“হ্যাঁ, তা-ই বলেছিলেন বটে।”
“বাজে কথা।”
“তার মানে ওই হিরে দুটো এক গুজরাটি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কেনা হয়নি?”
হরসুন্দরের মুখে দেখলুম হাসির রেখা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গালের চামড়া অল্প অল্প কঁপতে শুরু করেছে। মিনিট খানেক একেবারে নিঃশব্দে হেসে নিলেন তিনি। তারপর বললেন, “একটা সত্যিকথাকে চেপে রাখার জন্যে কত মিথ্যে কথাই না লোকে বলতে পারে। কোন মানে হয়?”
“সত্যি কথাটা কী?”
“সত্যি কথাটা এই যে, কোনও গুজরাটি ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ওই হিরে কেনা হয়নি।”
“তা হলে কার কাছ থেকে কেনা হয়েছে?”
আবার এক প্রস্ত হেসে নিলেন হরসুন্দর। এবারও সেই আগের মতোই নিঃশব্দে। তারপর বললেন, “কিনতে হবে কেন? ওই হিরে দুটো আদৌ কেনা হয়নি।”
সদানন্দবাবু অনেকক্ষণ কোনও কথা বলেননি। কিন্তু এরপরে আর তাকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না। সামনের দিকে মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে, ফিসফিস করে বললেন, “চোরাই মাল?”
“হতেই পারে। তবে কালীভূষণ চুরি করেননি।” হরসুন্দর বললেন, “আগের কথা জানি না, তবে এক্ষেত্রে ও দুটো চুরিও করা হয়নি, ডাকাতিও করা হয়নি।”
“তা কী করে হয়?” কৌশিক বলল, “আপনি বলছেন, এক্ষেত্রে ও দুটো কেনা হয়নি, আবার চুরি-ডাকাতিও করা হয়নি। হিরে দুটো কি তা হলে আপসে এসে গেল? তাও আবার হয় নাকি?”
“হবে না কেন, হয়।” কৌশিকের দিকে তাকিয়ে হরসুন্দর মুখুটি বললেন, “কিন্তু কী করে হয়, তুমি তো নেহাতই ছেলেমানুষ, তুমি সে কথা বুঝবে না।”
.
॥ ৬ ॥
ভাদুড়িমশাই বললেন, “মহিলাটি কে?”
চকিতে কৌশিকের দিক থেকে ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে মুখ ফেরালেন হরসুন্দর মুখুটি। দুই চোখের ধবধবে সাদা ভুরু দুটি একেবারে হঠাৎই তাদের স্বাভাবিক জায়গা থেকে আধ-ইঞ্চি উর্ধ্বে উঠে গেল। গলা ঈষৎ নামিয়ে তিনি বললেন, “ধরতে পেরেছেন দেখছি।”
ভাদুড়িমশাই সামান্য হেসে বললেন, “ঠিক যে ধরতে পেরেছি তা বলব না। তবে হ্যাঁ, আন্দাজ করেছি। কিন্তু আন্দাজ দিয়ে তো কাজ চলে না, আপনার কাছে সবটা জানতে চাই।”
“আমিও কি আর তেমনভাবে জানি যে, সাক্ষ্যপ্রমাণ সাজিয়ে সব বলব?” হরসুন্দর বললেন, “না মশাই, তা আমি জানি না। পাথুরে কোনও প্রমাণও আমি দাখিল করতে পারব না। তবে হ্যাঁ, দুয়ে-দুয়ে যে চার হয়, তার কি কোনও প্রমাণ লাগে?”
“তা লাগে না বটে!”
“তো সেইভাবে একটা থিয়োরি আমি দাঁড় করিয়েছি।” হরসুন্দর বললেন, “তার খানিক-খানিক অবশ্য গেস্-ওয়ার্ক। বিশেষ করে কালীভূষণের মৃত্যুর ব্যাপারটা।”
“বেশ তো, সেটাই বলুন।”
“খোলাখুলি বলব না, শুধু কু ধরিয়ে দেব। কিন্তু তার আগে দুটো কথা আপনাদের মনে রাখতে হবে। শ্যারশে লা ফাম বলে একটা প্রবাদবাক্য আছে জানেন তো?”
“জানি।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “ওটা ফরাসি প্রোভার্ব। এর অর্থ হচ্ছে মেয়েটাকে খুঁজে বার করুন। মানে, ধরেই নেওয়া হয় যে, তাবৎ জটিল রহস্যের মূলে রয়েছে কোনও মেয়ে। রহস্যের কিনারা করতে হলে সেই মেয়েটাকে খুঁজে বার করা চাই।”
হরসুন্দর বললেন, “কারেক্ট। কিন্তু শুধু এই কথাটা জানলেই তো হবে না। মনে রাখতে হবে আর-একটা কথাও।”
“সেটা কী?”
“ফাম ফাতাল কথাটা কখনও শুনেছেন?”
“শুনেছি। এটাও ফরাসি কথা।”
“অর্থ জানেন?”
“জানি। ইংরেজিতে এর অর্থ হল ফেটাল উয়োম্যান। সংস্কৃতে ওই যে বিষকন্যা বলে একটা কথা আছে, এ হল তা-ই। বাংলায় বলতে পারি; সর্বনাশা মেয়ে। যাব ঘাড়ে চাপে, তার সর্বনাশ করে ছাড়ে। …কিন্তু ব্যাপারটা কী মুখুটিমশাই? আপনি কি আমার ফরাসি বিদ্যের পরীক্ষা নিচ্ছেন নাকি?”
হরসুন্দর মুখুটি এতক্ষণ নিঃশব্দে হাসছিলেন। এবারে শব্দ করে হাসলেন। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, “আরে না। এককালে যে এখানে ফরাসি বিদ্যের বেশ ভালরকম চর্চা হত, যেমন পণ্ডিচেরিতে তেমনি এখানে..মানে ভদ্রেশ্বরে নয়, চন্নননগরে সেটা জানেন তো?”
“তা কেন জানব না?” ভাদুড়িমশাই বললেন, “ফরাসি কলোনি, সেখানে ফরাসি ল্যাংগুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচারের চর্চা হবে, সেটাই তো স্বাভাবিক।”
“ঠিক কথা। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, যারাই চননগরের বাসিদে, তারাই ফরাসিতে এক-একজন মস্ত পণ্ডিত। আবার ফরাসি কলোনির বাইরের লোক হলেই যে সে ফরাসি ভাষা জানবে না, তাও কিন্তু নয়।“
আলোচনা যে কোন দিকে যাচ্ছে, আমরা কেউই তা ঠিকমতো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তবে হরসুন্দরের প্রতিটি কথাতেই আমরা মাথা নেড়ে সায় দিয়ে যাচ্ছিলুম। সদানন্দবাবু অবশ্য শুধু মাথা নেড়েই ক্ষান্ত থাকার পাত্র নন। মাথা নাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তিনি মাঝে-মাঝেই বলছিলেন, “তা তো বটেই, তা তো বটেই।”
হরসুন্দর হয়তো সেই কারণেই ধরে নিয়ে থাকবেন যে, আমাদের মধ্যে সদানন্দবাবুই তার কথাবার্তার সবচেয়ে বড় বোদ্ধা। সরাসরি এবারে সদানন্দবাবুর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, “এই আমার কথাই ধরুন। আমি ভদ্রেশ্বরের লোক, কিন্তু ফরাসিটা আমি যে শুধু বুঝতে পারি, পড়তে পারি আর বলতে পারি, তা নয়, ওতে আমি যেমন আমার অটোবায়োগ্রাফি আর একখানা নাটক, তেমনি তিন-তিনখানা উপন্যাসও লিখে ফেলেছি।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “ছেপে বেরিয়েছে?”
“এখনও বেরোয়নি।” হরসুন্দর বললেন, “আশে কোম্পানির নাম শুনেছেন? ইংরেজরা ওই যাকে হ্যাঁচেট বলে আর কি। শুনেছেন?”
“তা কেন শুনব না? ডাকসাইটে ফ্রেঞ্চ পাবলিশার।”
“ঠিক বলেছেন। তো তাদের কাছে ম্যানাসক্রিপট পাঠিয়ে দিয়েছি। তারা পড়ে দেখছে। ছাপবে নিশ্চয়।”
ভদ্রলোক আরও কিছু বলতেন হয়তো, কিন্তু যে মেয়েটি চা দিয়ে গিয়েছিল, সে এই সময়ে ফের ঘরে ঢুকে বলল, “দাদু, তোমার বেড়াতে যাবার সময় হয়েছে। লাঠিটা এনে দেব?”
“আজ একটু পরে বেরোব।” হরসুন্দর বললেন, “কাপগুলো নিয়ে যা।” শূন্য পেয়ালাগুলিকে থালায় তুলে নিয়ে মেয়েটি নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।
ভদ্রলোকের বেড়াতে যাবার সময় হয়েছে শুনে আমরাও উঠে পড়তে যাচ্ছিলুম, কিন্তু হরসুন্দরই আমাদের বাধা দিয়ে বললেন, “আরে বসুন, বসুন, আসল কথাটাই তো এখনও বলিনি।…ও হ্যাঁ, কী বলছিলাম যেন?”
সদানন্দবাবু বললেন, “আপনার বই ছাপার কথা।”
“না, না, ওটা নয়। তার আগে কী বলছিলাম?”
পরমেশ বললেন, “বলছিলেন যে, আমরা চননগরের লোকেরাও সবাই ফরাসি জানি না, আবার আপনি ভদ্রেশ্বরের লোক হয়েও…”
কথাটা শেষ করতে দিলেন না হরসুন্দর। বললেন, “ঠিক ঠিক। আমি যা ফরাসি জানি, তোমাদের অনেকেই তার সিকির সিকিও জানো না।…কী, বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ, তা হলে ওই সেনেদের কথাই ধরো।”
বলেই হঠাৎ ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে তাকালেন হরসুন্দর মুখুটি। বললেন, “ও মশাই, ওই সেনেদের বাড়ি নিয়েই তো কথা হচ্ছিল, তাই না?”
“হ্যাঁ,” ভাদুড়িমশাই বললেন, “টু বি প্রিসাইজ, ওদের হরপার্বতীর চোখের হিরে নিয়ে।”
“ঠিক হিরে নিয়েও নয়, হিরে দুটো কী করে ওদের হাতে এল, তা-ই নিয়ে। কিন্তু আমিই বা সে-কথা জানলুম কী করে? আরে মশাই, আমিও জানতে পারতাম না, কালীভূষণের ধারাটা যদি ওবাড়িতে বজায় থাকত।..কী, এর থেকে কিছু বুঝলেন?”
কিছুই বুঝলুম না। অন্যদের দিকে তাকিয়ে মনে হল, তারাও কিছুই বোঝেননি। একা সদানন্দবাবুই শুধু মুখে একটা বুঝি-বুঝি ভাব জাগিয়ে রেখে মৃদু-মৃদু হাস্য করছেন।
ওই হাসিটাই তাঁর বিপদ ঘটাল। হরসুন্দর সরাসরি তার দিকে তাকিয়ে বললেন, “যাক, আপনি অন্তত বুঝেছেন।”
হাসিটা একেবারে সঙ্গে-সঙ্গেই সদানন্দবাবুর মুখ থেকে মুছে গেল। কাতর গলায় তিনি বললেন, “আজ্ঞে না।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “দেখুন হরসুন্দরবাবু, এর মধ্যে যে একজন মহিলা জড়িয়ে আছে, সেটা আমি আগেই আন্দাজ করেছিলুম। সম্ভবত তিনি বিমলভূষণের প্রপিতামহী শান্তিলতা দেবী। কিন্তু কালীভূষণের ধারা’ বলতে যে আপনি কী বোঝাতে চাইছেন, সেটা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। একটু যদি বুঝিয়ে বলেন তো বড্ড ভাল হয়।”
হরসূন্দর বললেন, “বলছি, বলছি। হিরে দুটো কোত্থেকে কীভাবে এল, তা তো আমাকে বলতেই হবে। তার প্রমাণও আমার কাছে রয়েছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, প্রমাণটাই বা আমার হাতে এল কীভাবে। আপনারা কি কালীভূষণের কথা কিছু জানেন?”
“এইটুকু জানি যে, তিনি বিত্তশালী মানুষ ছিলেন। ভাদুড়িমশাই বললেন, “শুনেছি যে, ওই মন্দিরের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। এও শুনেছি যে, তিনি গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মারা যান।”
“ঠিকই শুনেছেন। তবে ওই মারা যাওয়াটা নেহাতই দুর্ঘটনা, না আত্মহত্যা, তাই নিয়ে সেকালে কিছু মতভেদ ছিল বলে আমার বাপ-ঠাকুর কাছে শুনেছি। সে যা-ই হোক, কালীভূষণ যে ফরাসিটা খুব ভাল জানতেন, এটা আপনারা শুনেছেন?”
‘না। তবে জানাই তো স্বাভাবিক।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “ফরাসি এলাকায় থাকতেন, ফরাসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের আনুকূল্যে নিজের বিত্তসম্পদ যথাসম্ভব বাড়িয়ে নিয়েছিলেন, তাদের মন জুগিয়ে চলতে হত, তাদের ভাষাটা না জানলে চলে?”
“সে তো ঠিক,” হরসুন্দর হেসে বললেন, “ফরাসিদের সঙ্গে যার কাজ-কারবার, মেলামেশা, ওঠাবসা, ফরাসি ভাষায় তাকে দুরস্ত হতে হবে বই কী। কিন্তু না, কথাটা তো তা নয়।”
“কথাট। তা হলে কী?”
“কথাটা এই যে, কালীভূষণকে তো তার নিজের স্বার্থে …মানে নিজের কাজ কারবারের স্বার্থে ফরাসিতে দুরস্ত হতে হয়েছিল। কিন্তু তার স্ত্রীকে তাই বলে ফবাসি শেখাবার দরকার হল কেন?”
“বটে?” ভাদুড়িমশাই বললেন, “শান্তিলতাও ফরাসি জানতেন নাকি?”
“নামটাও জানেন দেখছি।”
“হ্যাঁ, জানি।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “বিমলভূষণের কাছে শুনেছিলুম। সেনেদের বাড়ির বিমলভূষণকে তো আপনি ভালই চেনেন?”
“তা চিনি বই কী।” হরসুন্দর তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন, “ওটা না-শিখেছে ফরাসি, না-শিখেছে ইংরেজি। বাংলাটাও ঠিকমতো শিখেছে কি না, তাতে আমার সন্দেহ আছে। ওটা একটা গাধা। ওর বাবা চন্দ্রভূষণ ছিল আমার ছেলেবেলার বন্ধু। তবে সেটাও ছিল একটা গাধা। লেখাপড়ায় ডডনং। ফরাসিদের একোলে পড়ত, কিন্তু ক্লাস ফোর
থেকে ফাইভে উঠতেই বার তিনেক তার প্রোমোশন আটকে যায়। ভাবতে পারেন?”
সদানন্দবাবু বললেন, “একোলটা কী জিনিস।“
“ইস্কুল।” হরসুন্দর বললেন, “কিন্তু যা বলছিলাম। কালীভূষণের পরে ও-বাড়িতে আর লেখাপড়ার চর্চা হয়নি। ওরা না জানে ফরাসি, না জানে ইংরেজি।” একটুক্ষণের জন্যে চুপ করলেন হরসুন্দর। তারপর বললেন, “কীর্তিভূষণ সম্পর্কে শুনেছি, তিনি তবু তাঁর মায়ের চাপে পড়ে একটু-আধটু ফরাসি শিখেছিলেন। কিন্তু চন্দ্রভূষণ তো আ-বে-সে দে’র পরে আর কিছুই শেখেনি। আরে মশাই, ফরাসি জানলে কি আর ফ্রান্স থেকে লেখা একখানা চিঠি পড়াবার জন্যে তাকে আমার কাছে ছুটে আসতে হত। আর সেই চিঠি না পড়লে কি আমিই জানতে পারতুম যে, ওদের হিরে দুটো কোত্থেকে কীভাবে এসেছিল?”
ভাদুড়িমশাইয়ের চোখ দুটো দেখলুম হঠাৎই সরু হয়ে এসেছে। বললেন, “চিঠিখানা কোথায়?”
“আমারই কাছে আছে। তবে কাউকে দেখাইনি। কথা ছিল, চিঠিখানা পড়ে বাংলায় আমি তার তর্জমা করে রাখব, চন্দ্রভূষণ তার পরদিন এসে তর্জমা আর মূল চিঠি আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে। কিন্তু তা আব সে নিতে পারেনি। সেই রাত্তিরেই বাড়িতে ফিরে তার জ্বর আসে। কী জ্বর তা বোঝা গেল না। তিন দিনের মধ্যে চন্দ্র মারা গেল।”
“এটা কবেকার কথা?”
“নাইনটিন সেভেন্টির। তার মানে প্রায় তিরিশ বছর আগেকার।”
“চিঠিখানা দেখা যায়?”
“স্বচ্ছন্দে।” হরসুন্দর বললেন, “চান তো সঙ্গে করে নিয়েও যেতে পারেন। তবে কিনা ফেরত চাই। ফরাসি ভাষায় চন্দননগরের একটা ইতিহাস লিখছি কিনা, ডকুমেন্টারি এভিডেন্স হিসেবে ওটা কাজে লাগবে।”
চিঠি সম্পর্কে তক্ষুনি আর-কিছু বললেন না ভাদুড়িমশাই। প্রসঙ্গ পালটে বললেন, “শান্তিলতাকে ফরাসি শেখাবার কথা হচ্ছিল। তা এতে তো আমি অস্বাভাবিক কিছু দেখছি না। কালীভূষণের সঙ্গে তখনকার ফরাসি কর্তাদের যে দহরম-মহরমের কথা শুনেছি, তাতে তো মনে হয়, তাদের দেওয়া পার্টি-টার্টিতেও তাকে যেতে হত। মিল্ড পার্টি হলে গিন্নিকেও হয়তো নিয়ে যেতেন..। মানে সেটাই তো স্বাভাবিক। আর গিন্নি যদি যানই, তো ভাষা না জানার দরুন সেখানে গিয়ে তিনি বোবা হয়ে বসে থাকবেন, তা তো হয় না। তা সে যা-ই হোক, ফরাসিটা তিনি শিখলেন কোথায়? এখানকারই কোনও ইস্কুলে, না তার স্বামীর কাছে?”
হরসুন্দর হেসে বললেন, “পার্টি-টাটির কোনও কথাই উঠছে না, এমনকী ইস্কুলেরও না। আমার ঠাকুমার কাছে শুনেছি যে, শান্তিলতা ছিলেন…. ওই যাকে ঘোর পর্দানশিন মহিলা বলে, তা-ই। আর তার স্বামী? যে-লোককে সম্পত্তি বাড়ানোর কাজেই অষ্টপ্রহর ব্যস্ত থাকতে হয়, স্ত্রীকে ফরাসি শেখাবার সময় কোথায় তার?”
“তা হলে তিনি ফরাসিটা শিখলেন কোথায়?”
“সেই কথাই তো বলছি।” হরসুন্দর আবার নিঃশব্দ হাসতে শুরু করলেন। তারপর বললেন, “টাকাপয়সার তো অভাব নেই, স্ত্রীকে ফরাসি শেখাবার জন্যে কালীভূষণ তার বাড়িতেই একজন টিউটর রেখে দিলেন।”
“লোকটা ফরাসি?”
“অবশ্য। লোকটা গ্রেনাডিয়ার হয়ে এসেছিল, কিন্তু শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্যে ফ্রেঞ্চ আর্মি থেকে তার চাকরি যায়। তখন কালীভূষণ তাকে বাড়িতে আশ্রয় দেন। আর এতকাল যাঁকে বন্ধ্যা ভাবা হয়েছিল, সেই শান্তিলতা সন্তানসম্ভবা হন। …তো যা বুঝবার, এর থেকেই বুঝে নিন আপনারা। বাকি যা বুঝবার, চিঠিটা পড়লেই বুঝতে পারবেন। আমি বরং চিঠিটা নিয়ে আসি।”
হরসুন্দর ভিতরে গিয়ে মিনিট তিন-চারের মধ্যেই ফিরে এলেন। হাত বাড়িয়ে ভাদুড়িমশাইয়ের হাতে একটা খাম ধরিয়ে দিয়ে বললেন, “এই সেই চিঠি।… ক যা পাবার, এরই মধ্যে পেয়ে যাবেন। আর হ্যাঁ, চিঠিটা পড়তে পড়তে হয়তো অর্লভ ডায়মন্ডের কথা আপনাদের মনে পড়তে পারে। সেটা ছিল চোরাই হিরে।”
বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছি, হঠাৎ একটি অল্পবয়সী বউ একেবারে ঝড়ের মতো এসে হরসুন্দর মুখুটির বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। ঢুকেই তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল, “ও দাদু, এ
কী সর্বনাশ করলেন আপনি?”
হরসুন্দর বাড়ির বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। সেখান থেকেই হতভম্ব গলায় বললেন, “কেন, কী করেছি?”
“পটলার চুল কেটে দিলেন কেন?” কপাল চাপড়ে বউটি বলল, “ও তো মানতের চুল! সামনের জষ্টি মাসে যষ্ঠীতলায় গিয়ে ওর চুল ফেলার কথা! এ কী সর্বনাশ হল!”
.
॥ ৭ ॥
গলির পথটুকু তাড়াতাড়ি পেবিয়ে এসে গাড়িতে উঠে পড়লুম আম। ভাদুড়িমশাই সেলফের চাবি ঘুরিয়ে গাড়িতে স্টার্ট দিলেন। পরমেশ চৌধুরির বাড়িতে এসে পৌঁছনো পর্যন্ত পথে একটিও কথা হল না। বাড়িতে ঢুকে ভাদুড়িমশাই বললেন, “চিঠিখানা পড়তে হবে, এখন খানিকক্ষণ আমি একটু একলা থাকতে চাই। .. পরমেশ, তুমি এদের সঙ্গে বসে গল্প করো, আমি পাশের ঘরে আছি।”
ড্রয়িং রুমের লাগোয়া পুব দিকের ঘরটা ভাদুড়িমশাই আর কৌশিকের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি সেখানে ঢুকে গেলেন
সদানন্দবাবু খুব বেশিক্ষণ কথা না বলে থাকতে পারেন না। এতক্ষণ তিনি একটাও কথা বলেননি। এইবারে কৌশিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, “মানুষ বুড়ো হলে কী হয় বলে দিকি?”
কৌশিক বলল, “তা আমি কী করে বলব? আমি কি বুড়ো হয়েছি? ও-সব আপনারাই ভাল বুঝবেন।”
পরমেশ ক্লিষ্ট হেসে বললেন, “বুড়ো হলে বাতগ্রস্ত হয়।”
“আরে ধুর মশাই, সদানন্দবাবু বললেন, “আপনার কতা হচ্ছে না, আপনি, তো ছেলেমানুষ। কত বয়েস হল আপনার?”
“সিক্সটিটু।”
“ওটা কি একটা বয়েস হল নাকি? এই যে আমি সেভেন্টি পেরিয়ে এইচি, তাও নিজেকে বুড়ো ভাবি না। আমার ওয়াইফ অবিশ্যি গেঁটেবাতে একটু কাবু হয়ে পড়েছেন, কিন্তু আমি?” সদানন্দবাবু চেয়ার ছেড়ে তড়াক করে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, “রোজ তিন মাইল মর্নিং ওয়াক করি।”
আমি বললুম, “ও নিয়ে এত জাঁক করবেন না। হরসূন্দরবাবুর বয়েস তো শুনলেন, বিরানব্বই, তা মর্নিং ওয়াক তো তিনিও নাকি করেন। বাতগ্রস্ত হতে পারতেন?”
কৌশিক বলল, “সত্যি, এত বয়েস ভদ্রলোকের, অথচ এখনও দিবি। সটান। ভাবা যায়? মেমারিও তো মনে হল ঠিকই আছে।”
“শুধু মেমারি কেন, পরমেশ বললেন, “চোখ, কান, নাক, সব ঠিক আছে। তা ছাড়া, দেখলেই তো, একেবারে ফোটোগ্রাফিক মেমারি। খাওয়া-দাওয়াও একদম স্বাভাবিক। বুড়ো হলে শুনেছি হজমশক্তি কমে যায়। ওঁর খাওয়া দেখে তা কিন্তু মনে হয় না। প্রতিটি নেমা অ্যাটেন্ড করেন, খানও পংক্তিভোজনে বসে…। না, এত যে বয়েস, হাঁটা-চলা খাওয়া-দাওয়া, কোনও কিছু দেখেই তা বুঝবার উপায় নেই।”
সদানন্দবাবু বললেন, “দাত দেকলুম একটাও নেই। বাঁদিয়ে নেন না কেন?”
“দরকার হয় না।” পরমেশ বললেন, “যে-লোক স্রেফ মাড়ি দিয়ে চিবিয়ে সজনে ডাটা ছিবড়ে করে ফেলতে পাবে, তার আবার নকল-দাঁতের দরকার কী…. তবে হ্যাঁ, বার্ধক্যের একটা লক্ষণ অবশ্য বছর খানেক হল দেখা দিয়েছে। পকেটে সব সময় একটা কঁচি নিয়ে ঘোরেন। রাস্তায় বেরিয়ে একবার দেখতে পেলেই হল যে, কোনও বাচ্চা ছেলেব চুল তার কাধ অব্দি নেমে এসেছে, বাস, কাঁক করে তাকে ধরে অমনি পকেট থেকে কাচি বার করে ঘাচ-গ্র্যাচ করে তার চুল কাটতে বসে যাবেন। তার ফলে কী হয়, সে তো আপনারা একটু আগেই আজ দেখলেন। মানতেব চুল কেটে ফেলেছে, বাচ্চাটার মা কি ওঁকে সহজে ছেড়ে দেবে?”
কৌশিক বলল, “বাতিকগ্রস্ত আর কাকে বলে!”
সদানন্দবাবু বললেন, “আমার পিসশ্বশুরের সঙ্গে হরসূন্দরবাবুব খুব মিল আচে দেকচি। বুড়ো বয়সে তিনিও তার ফতুয়ার পকেটে কঁচি নিয়ে ঘুরতেন।”
“বলেন কী, কৌশিক আঁতকে উঠে বলল, “তিনিও বাচ্চা-ছেলেদের ধরে চুল কেটে দিতেন?”
‘না, চুল নয়… মানে চুলই, তবে গোটা মাতার চুল নয়, সদানন্দবাবু বললেন, “শুদু টিকি। একবার তো সরস্বতী পুজোর দিনে, গুটিগুটি পেছন দিক থেকে গিয়ে, ঘ্যাঁচ করে এক পুরুতঠাকুরের টিকি কেটে দিয়েছিলেন।”
“অ্যাঁ, বলেন কী?”
“সে মানে কেলেঙ্কারির একশেষ! পুরুতঠাকুর তো হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদেন আর বলেন যে, তার মিনস অফ লাইভলিহুডই চলে গেল। যে পুরুতের টিকিই নেই, কে তাকে পুজো করতে ডাকবে!…তো শেষ পর্যন্ত কী হল জানেন?”
পরমেশ বললেন, “কী হল?”
“পিসতুতো শালাকে নগদ ফিফটি রুপিজ দিয়ে ব্যাপারটা মেটাতে হল।” সদানন্দবাবু বললেন, “আজ যা কাণ্ড দেকলুম, তাতে মনে হচ্চে হরসুন্দরবাবুকেও তার গাঁট থেকে কিছু খসাতে হবে। মানতের চুল কেটেচেন, তার দণ্ড দিতে হবে না?”
আমি বললুম, “পাড়ার ছেলেরা ওঁর পিছনে লাগে না?”
“লাগে বই কী, পরমেশ বললেন, “আড়ালে-আবডালে বলে, হরসুন্দর না নরসুন্দর!”
সদানন্দবাবু বললেন, “তাও তো আমার বাবার এক মামাতো ভাইয়ের কতা এখনও বলিনি। তিনি ছিলেন…”
তিনি যে কী ছিলেন, তা আর শোনা হল না, কেন না ঠিক সেই মুহূর্তেই পাশের ঘর থেকে ভাদুড়িমশাই বেরিয়ে এসে, হরসুন্দরবাবুর কাছ থেকে সংগৃহীত চিঠিখানা পরমেশবাবুর দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, “তুমি তো ফরাসি জানো, চিঠিখানা পড়ে দ্যাখো তো কী মনে হয়।”
চিঠির ভাঁজ খুলে একবার মাত্র চোখ বুলিয়েই সেটা আবার ভাদুড়িমশাইকে ফিরিয়ে দিলেন পরমেশ। বললেন, “ওরে বাবা, এ তো দেখছি কাগের ঠ্যাং আর বগের ঠ্যাং! এ হাতের লেখা আমি পড়তে পারব না। তুমি পেরেছ?”
“পেরেছি বললে বাড়িয়ে বলা হবে।” ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, “শুধু যে হাতের লেখাটাই কদর্য, তা তো নয়, বানান জানে না, ব্যাকরণ অশুদ, চিঠিখানা যার লেখা, সে যে ঘোর অশিক্ষিত লোক, তাতে সন্দেহ নেই। টেনেবুনে একটা অর্থ অবশ্য করেছি।”
এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন ভাদুড়িমশাই। তারপর বললে “অবশ্য পরিষ্কার কোনও অর্থ যে এ-ক্ষেত্রে থাকবেই, এমন আশা করাটাই হয়তো বোকামি হয়ে যাচ্ছে।”
পরমেশ বললেন, “কেন?”
ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, “তোমার প্রশ্ন থেকেই বুঝতে পারছি যে, চিঠির উপরকার ঠিকানাটাও তুমি দ্যাখোনি। নাও, সেটা অন্তত পড়ে দ্যাখো।”
হাত বাড়িয়ে ভাদুড়িমশাইয়ের কাছ থেকে চিঠিখানা আবার নিলেন পরমেশ। তারপর ঠিকানায় চোখ বুলিয়েই কৌতুকের সঙ্গে বিস্ময় মেশানো একটা ভঙ্গি করে বললেন,
“ওরেব্বাবা, এ তো পাগলাগারদ থেকে লেখা!”
কৌশিক বলল, “কী হচ্ছে মামাবাবু, আমরা ফরাসি জানি না বলে কি তোমরা দুজনে শুধু নিজেদের মধ্যেই হাসাহাসি করবে নাকি? আমাদেবও একটু বুঝিয়ে বলল।”
“বলছি।” ভাদুড়িমশাই এতক্ষণ দাঁড়িয়ে-পঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। এবারে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বার করে একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর মুখ থেকে গলগল করে একরাশ ধোঁয়া বার করে বললেন, “এইক্স-এর নাম শুনেছিস?”
“না।” কৌশিক বলল, “ওটা কী বস্তু? খায়, না গায়ে মাখে?”
রসিকতাটাকে আমল না-দিয়ে ভাদুড়িমশাই বললেন, “দক্ষিণ ফ্রান্সের বন্দর মার্শাইয়ের নাম তো শুনেছিস, এই শহরটা তার খুব কাছেই। এই চিঠিটা সেখানকার….”
কথাটা লুফে নিয়ে কৌশিক বলল, “সেখানকার এক পাগলাগারদ থেকে লেখা হয়েছে, এই তো?”
“পাগলাগারদ নয়,” ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, “পরমেশ ওটা মজা করে বলছিল। আসলে লেখা হয়েছে এইক্স-এর একটা প্রাইভেট নার্সিং হোম থেকে। সেখানে অবশ্য সব রকমের রোগীদের নেওয়া হয় না, ভর্তি করা হয় শুধু মেন্টাল পেশেন্টদের।”
“তো সেই নার্সিংহোম থেকে একজন পেশেন্ট এই চিঠি লিখেছে?”
“হ্যাঁ।”
“কী লিখেছে?” ভাদুড়িমশাই এই প্রশ্নের উত্তরে যা বললেন, সংক্ষেপে সেটা এইরকম :
চিঠির তারিখ সম্পর্কে হরসুন্দর ভুল বলেননি। এ-চিঠি ১৯৭০ সালেই লেখা বটে। যিনি লিখেছেন, তাঁর নাম লুই আঁতোয়ান। তিনি জানাচ্ছেন যে, বাজারে তার দেনার পরিমাণ আড়াই লাখ ফ্রা। ছ’মাসের মধ্যে যদি না এই দেনা মেটাতে পারেন, তা হলে পাওনাদারেরা তাকে জেলে পাঠাবে। মাদাম শান্তিলতা সেন যদি আজ বেঁচে থাকতেন, তা হলে তার পুরনো বন্ধু পিয়ের আঁতোয়ানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক হিসেবে পিয়েরের নাতির এই দুর্দিনে তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতেন নিশ্চয়। কিন্তু মাদাম অথবা তার পুত্র কীর্তিভূষণ তো বেঁচে নেই, তাই বাধ্য হয়ে তাকে মাদামের নাতি চন্দ্রভূষণকে এই চিঠি লিখতে হচ্ছে। চন্দ্রভূষণ যদি আড়াই লাখ ফ্রাঁ অথবা তার সমমূল্যের ডলার, পাউন্ড কিংবা অন্য কোনও ইয়োরোপীয় মুদ্রার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, পত্রলেখক তা হলে রক্ষা পান। একই সঙ্গে, খুবই বিনীতভাবে হলেও, লুই আঁতোয়ান চন্দ্রভূষণকে এ-কথা জানিয়ে দিতে ভোলেননি যে, পিয়ের আঁতোয়ান মাদাম শান্তিলতাকে একটি উপহার দিয়েছিলেন, যে-উপহারের আর্থিক মূল্য আড়াই লাখ ফ্রার চেয়ে বেশি ছাড়া কম হবে না।
কথা শেষ করে পরমেশের দিকে তাকিয়ে ভাদুড়িমশাই বললেন, “কোন উপহারের কথা বলা হচ্ছে বুঝতে পারছ?”
পরমেশ প্রায় খাবি খাওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, “এই হিরেজোড়া?” ভাদুড়িমশাই মৃদু-মৃদু হাসছিলেন। বললেন, “তা-ই তো মনে হয়।”
“ওরে বাবা,” সদানন্দবাবু বললেন, “হরসূন্দর মুখুটি তো তা হলে মিচে কত কননি। কিন্তু একটা কতা তো মশাই আমি ঠিক বুজে উঠতে পারছি না।”
“কোন কথাটা?”
“লোকটা..মানে ওই পিয়ের তত ছিল গ্রেনাডিয়ার। হরসুন্দরবাবু অন্তত সেই কতাই বলেছেন। তার মানে তো সেরেফ একজন সোলজার। তা সোলজার হয়ে সে অত দামি হিরে পেল কোতায়? আর হ্যাঁ, পেলই বা কীভাবে?”
“সেটাও কিন্তু হরসুন্দরবাবুই বলেছেন।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “মানে সরাসরি বলা তো আর তার পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি কি গণতকার যে, অদ্দিন আগে কে কীভাবে একজোড়া হিরে জোগাড় করেছিল, খড়ি পেতে আঁক কষে সেটা বলে দেবেন। না মশাই, সেইভাবে তিনি কিছু বলেননি। তবে হ্যাঁ, একটা আন্দাজ দিয়েছিলেন ঠিকই।…তার শেষ কথাটা মনে নেই?”
“কী যেন একটা ডায়মন্ডের কথা বলেছিলেন।” কৌশিক বলল, “এও বলেছিলেন যে, সেটা ছিল চোরাই হিরে।”
“ঠিকই বলেছিলেন।”ভাদুড়িমশাই বললেন, “যে অলভ ডায়মন্ডের জগৎজোড়া খ্যাতি, সেটা তো এখন ক্রেমলিনে রয়েছে, কিন্তু এইটিনথ সেঞ্চুরিতে সেটা কোথায় ছিল জানিস?”
“কোথায় ছিল?”
“সাউথ ইন্ডিয়ার এক মন্দিরে। আদতে সেটাও ছিল বিগ্রহের চোখ। সেভেন্টিন ফিফটিতে সেটা চুরি হয়ে যায়। তাজ্জব ব্যাপার কী জানিস, সেটাও একজন ফ্রেঞ্চ সোলজারই চুরি করেছিল। এ-হাত সে-হাত ঘুরে সেটা কাউন্ট গ্রিগরি অর্লভের হাতে গিয়ে পৌঁছয়। বাস, সেই থেকে তার নাম হয়ে গেল অর্লভ ডায়মন্ড।
সদানন্দবাবু হাঁ করে সব শুনছিলেন। ভাদুড়িমশাই চুপ করতেই হা বন্ধ করে তিনি আমার দিকে তাকালেন। আমি বললুম, “কী ভাবছেন?”
“ভাবছি যে, এই হিরেজোড়াও চোরাই মাল নয় তো?”
“হতেই পারে।” ভাদুড়িমাশাই বললেন, “এ দুটোও হয়তো কোথাও কোনও বিগ্রহেরই চোখ ছিল। পিয়ের আঁতোয়ান সেখান থেকে হাপিস করে চন্দননগরে চলে আসে।”
“তা তো বুজলুম।” সদানন্দবাবু বললেন, “কিন্তু তত দামি জিনিস সে শান্তিলতাকে উপহার দিতে গেল কেন? বাপ রে, কতায় বলে সাত রাজার ধন এক মাণিক্য। আর এ তো একজোড়া। চোদ্দো রাজার ধন বললেই হয়। দুম করে সেটা সে কিনা একজন ইন্ডিয়ান লেডিকে দিয়ে ক্লি। ভাবা যায়? কী ব্যাপার বলুন তো?”
ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, “থাক, থাক্, ও নিয়ে আব গবেষণা করে লাভ নেই। দিয়েছে, বেশ করেছে। আর তা ছাড়া, এমন একজনকেই তো দিয়েছে, বুড়ো বয়সেও যার সেবা যত্নের কথা সে ভুলতে পারেনি। সত্যিই পারেনি। নয়তো নাতির কাছে পিয়ের কেন বারেবারে সেই সেবাযত্নের গল্প করবে? না না, মিথ্যে বলছি না। লুই তার চিঠিতেই তা জানিয়েছে।”
চিঠিখানা খুলে ধরলেন ভাদুড়িমশাই। তা থেকে লাইন দুয়েক পড়ে শোনালেন। তারপর বললেন, “যচ্চিলে, আপনারা তো আবার ফরাসি বুঝবেন না।…. ওহে পরমেশ, তুমি এই জায়গাটা পড়ে এঁদের একটু বাংলায় বুঝিয়ে বলল তো।’
পরমেশ হেসে বললেন, “আমি ফরাসি জানি ঠিকই, কিন্তু ওই হাতের লেখার পাঠোদ্ধার করতে পারব না। তুমিই বুঝিয়ে বলে, চারুদা।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “তা হলে শুনুন। লুই লিখছে যে, তার ঠাকুর্দা তাদের কাছে প্রায়ই সেই দয়াবতী মহিলার অর্থাৎ শান্তিলতার গল্প করতেন। বলতে যে, তাঁর সেবাযত্নেরও তুলনা হয় না, আবার রান্নার হাতও ছিল অসাধারণ। শান্তিলতা তাঁকে যে পোয়র কারি বেঁধে খাইয়েছিলেন, তার স্বাদ নাকি তিনি বুড়ো বয়েসেও ভুলতে পারেননি।…বুঝুন।”
সদানন্দবাবু বললেন, “বুজলাম। কিন্তু পোয়র কারিটা কী বস্তু?” আমি হেসে বললাম, “মাছের ঝোল। ওইটুকু ফরাসি আমি জানি।”
.
॥ ৮ ॥
রাত এখন সাড়ে নটা। একটু আগে আমাদের নৈশাহার সমাধা হয়েছে। পাবদা মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেতে-খেতে সদানন্দবাবু একবার গম্ভীর গলায় বলেছিলেন, “পোয়াসঁর কারিটা দেকচি দিব্যি হয়েছে।” শুনে আমরা হেসেও উঠেছিল, তবে ডিনার টেবিলে এ ছাড়া আর অন্য কোনও কথা হয়নি। তারপরে আমরা এ-বাড়ির ছাতে এসে বসেছি। শুনেছি, ছাত থেকে গঙ্গা দেখা যায়। কিন্তু ঝড়বৃষ্টির নামগন্ধ না-থাকলেও হালকা মেঘে আকাশ ঢাকা, ফলে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। স্ট্র্যান্ডের দিক থেকে মাঝে-মাঝে এক-আধ ঝলক বাতাস ছুটে আসছে, তাতে মৃদু একটা ফুলের গন্ধও পাচ্ছি। এটাই কি জাকারাণ্ডার গন্ধ? কে জানে।
সদানন্দবাবু আর ছাত পর্যন্ত আসেননি। খাওয়ার পাট চুকে যাবার পরে বললেন, বড্ড ধকল গেছে, তিনি আর রাত জাগতে পারবেন না। ড্রয়িং রুমের পশ্চিম দিকের ঘরটা বরাদ্দ হয়েছে আমার ও সদানন্দবাবুর জন্যে। তিনি সেখানে চলে গেলেন।
খানিকটা সময় চুপচাপ কাটল। তারপর ভাদুড়িমশাই বললেন, “কৌশিক তো কাল ভোরের ট্রেনেই কলকাতা চলে যাচ্ছে, তোমাকে আর তার জন্যে কষ্ট করতে হবে না, পরমেশ, আমি এমনিতেই শেষ রাত্তিরে উঠে পড়ি, ওকে আমিই গিয়ে স্টেশনে ছেড়ে দিয়ে আসব।”
পরমেশ বললেন, “তোমাকেও কষ্ট করতে হবে না। আমি রিকশাওয়ালাকে বলে রেখেছি। চেনা লোক, সে-ই ঠিক সময়ে এসে ওকে নিয়ে যাবে।”
কৌশিক বলল, “তা তো হল, কিন্তু ঘুম থেকে আমাকে তুলে দেবে কে?”
“তার জন্যে তো আমিই আছি।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “ও নিয়ে ভাবিস না, তোকে তুলে দিয়ে তারপর আমি জগিং করতে যাব।”
“তা হলে আমিও নীচে গিয়ে শুয়ে পড়ি।” কৌশিক বলল, “তোমরা গল্প করো, আমি আর রাত জাগব না।”
কৌশিক নীচে চলে যাবার পর ভাদুড়িমশাই বললেন, “শোনো হে পরমেশ, এবারে দু’একটা কাজের কথা বলি। কৌশিক তো কাল ভোরের ট্রেনে চলে যাচ্ছে, আমরাও কাল তোমার এখানে ব্রেকফাস্ট করে তারপর সেনেদের বাড়িতে চলে যাব। পরশু সংক্রান্তি, সম্ভবত সাত-সকালেই হরপার্বতীর চোখে হিরের মণি পরানো হবে। হিরে যদি চুরি হয়ই, তো আমার ধারণা সেই সময়েই হবে। তার আগে গোটা জায়গাটা আমার একটু দেখে রাখা দরকার। বাড়ির লোকজনদেরও মোটামুটি চিনে রাখতে চাই। ও বাড়িতে কে কে থাকে, তুমি জানো?”
“তা কেন জানব না?” পরমেশ বললেন, “বিমলভূষণের ছেলে নেই, থাকার মধ্যে আছে একটি মেয়ে। তবে তার বিয়ে হয়ে গেছে, সে শ্রীরামপুরে তার শ্বশুরবাড়িতে থাকে। একটু দূর-সম্পর্কের এক ভাগ্নে অবশ্য তার বউ আর বাচ্চা নিয়ে বছর পাঁচেক আগে বিমলভূষণের কাছে এসে উঠেছিল, তখন থেকে তারা ওখানেই রয়ে গেছে। তাও বাড়িটা যেন খাঁ-খাঁ করে।”
“কেন?”
“সে তুমি বাড়িটা দেখলেই বুঝতে পারবে। বনেদি পরিবারের সেকেলে বিরাট বাড়ি। একতলা-দোতলা মিলিয়ে অগুন্তি ঘর। অথচ লোক মাত্র পাঁচজন। বিমলভূষণ, তার বউ কনক, ভাগ্নে নই, ভাগ্নে-বউ আর তাদের বছর আট-দশের একটি ছেলে। বাস।”
“বিমলভূষণরা কোন তলায় থাকে?”
“দোতলায়। দুটি তো প্রাণী। বিমল আর তার বউ। তবে ওদের মেয়ে-জামাই এই সময়ে আসে, তারা হয়তো এসে থাকতে পারে।”
“আর একতলায়?”
“একতলার একদিকে দুটো ঘর নিয়ে থাকে নটরা। বাকি ঘরগুলোতে চাকর-বাকরেরা থাকে।”
একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন ভাদুড়িমশাই। তারপর বললেন, “বিমলভূষণের আর্থিক অবস্থা কীরকম? কালীভূষণ শুনেছি বিস্তর জমিজমা করেছিলেন। কিন্তু জমিদারি প্রথা তো লোপ পেয়েছে, বিমলভূষণও খুব-একটা করিতকর্মা লোক বলে মনে হয় না। ওদের সোর্স অব ইনকামটা তা হলে কী?”
“সোর্স অব ইনকাম প্রচুর।” পরমেশ হেসে বললেন, “জমিদারি গেছে বলে তো আর তাবৎ স্থাবর সম্পত্তি লোপ পায়নি। এই চন্নননগরে ওদের বাড়ি রয়েছে তা অন্তত দশ বারোটা, বাজারে দোকানঘরও কিছু কম নেই। তার থেকে ভাড়া নেহাত কম মেলে না। তা ছাড়া ওই শিবমন্দির থেকেই কি ইনকাম কিছু কম হয় ভেবেছ? কালীভূষণ ওই একটা জিনিস বানিয়ে গেছেন বটে।”
“বুঝলুম।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “কিন্তু এতসব সম্পত্তি সামলে রাখার ঝামেলাও তো কিছু কম নয়। সে-সব কে করে?”
“এই নুটুই করে। বাড়ি আর দোকানঘরের ভাড়া আদায় থেকে মন্দিরের দর্শনী, প্রণামীর টাকাপয়সার হিসেব রাখা, বিল মেটানো, রসিদ দেওয়া, লোক লাগানো, মজুর খাটানো–মানে এ টু জেড–সবই ও একা করে।”
“মন্দির যখন আছে, তখন একজন পুজরি ঠাকুরও আছেন নিশ্চয়?”
“তা আছেন বই কী।”
“তিনি থাকেন কোথায়?”
“ওখানেই থাকেন। তবে মূল বাড়িতে থাকে না। বাড়ির বাইরে একটা গেস্ট হাউস আছে। তার একতলায় আর দোতলায় দুটো-দুটো করে চারটে ঘর। পুজুরি ঠাকুর থাকেন একতলায়। তোমরা সম্ভবত দোতলায় থাকবে।”
শুনে, আবার একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন ভাদুড়িমশাই। একটা সিগারেট ধরালেন। দেশলাই-কাঠিটাকে শূন্যে বার দুয়েক নেড়ে, নিবিয়ে, আঙুলের টোকা মেরে দুরে নিক্ষেপ করলেন। তারপর বললেন, “একটা কথা জিজ্ঞেস করি, পরমেশ। একটু ভেবেচিন্তে উত্তর দিয়ো। নুটু লোকটি কেমন?”
পরমেশ হেসে বললেন, “যে-ভাবে সব সামলাচ্ছে, তাতে তো বেশ ঝানু লোক বলেই মনে হয়। বিমলকে বলতে গেলে প্রায় কিছুই করতে হয় না, কাগজ এগিয়ে দিলে সই করেই খালাস, ভাগ্নেটাকে পেয়ে বেঁচে গেছে।… তা তোমরা কাল ব্রেকফাস্টের পরেই চলে যাবে কেন, অন্তত লাঞ্চটা করে তারপর যাও।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “না হে পরমেশ, আর তো সময়ই নেই, কাল সকালেই যাওয়া ভাল।”
এরপরে আর কথা বিশেষ হল না। আরও খানিকক্ষণ ছাতে বসে থেকে আমরা একতলায় নেমে এলুম। ঘরে ঢুকে দেখলুম, অল্প পাওয়ারের একটা হালকা নীল আলো জ্বালিয়ে রেখে সদানন্দবাবু অঘোরে ঘুমোচ্ছন।
নীল আলোটার দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকতে-থাকতেই একেবারে ঝট করে একটা কথা মনে পড়ল আমার। মার্ত্যা লুমিয়েরকে কলকাতায় প্রথম দেখার পর কৌশিক তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিল যে, লোকটির চোখের তারা নীল। কিন্তু শ্রীরামপুর ছাড়িয়ে একটা ধাবার সামনে যে মাতা লুমিয়েরকে আমরা দেখি, তার চোখের তারা মোটেই নীল নয়, বাদামি। লোকটাকে দেখার পর থেকেই যে কেন একটা অস্বস্তির কাটা আমার মনের মধ্যে খচখচ করছিল, এতক্ষণে সেটা বুঝতে পারা গেল।
.
॥ ৯ ৷৷
আজ তেরোই এপ্রিল, মঙ্গলবার। সারাটা দিন নানা কাজে আর হরেকরকম লোকের সঙ্গে কথা বলে কেটেছে। এরই মধ্যে বিকেলে একবার স্ট্র্যান্ড থেকেও এক চক্কর বেড়িয়ে আসা গেল। এখন রাত ন’টা বাজে। একটু আগে বিমলভূষণ, তার স্ত্রী ও মেয়ে জামাইয়ের সঙ্গে এঁদের বসতবাড়ির দোতলার ডাইনিং রুমে বসে রাতের খাওয়া সেরে নিয়েছি। তারপর চলে এসেছি এই গেস্ট হাউসের দোতলায়। দোতলায় দুটি ঘর। মাঝখানে বাথরুম। দুদিকের ঘর থেকেই বাথরুমে যাওয়া যায়। যে-দিক থেকেই যিনি যান, অন্য দিকের দরজাটা বন্ধ করে দিলেই হল।
এখন বলি, আজ সকাল থেকে কী কী ঘটেছে।
সকালের ট্রেনেই কৌশিক কলকাতায় ফিরে গেছে। শেষ রাত্তিরে স্ট্র্যান্ড থেকে জগিং সেরে এসে ভাদুড়িমশাই তাকে ঘুম থেকে তুলে দেন। রিকশাওয়ালাকে পরমেশ তো বলেই রেখেছিলেন, সেও ঠিক-সময়ে এসে কৌশিককে নিয়ে স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছে।
কথা ছিল পরমেশ চৌধুরির বাড়িতে ব্রেকফাস্ট করেই আমরা সরাসরি সেনেদের বাড়িতে চলে আসব। ব্রেকফাস্ট শেষ করি সাড়ে আটটায়। মহকুমা সদর হলেও চন্দননগর যে খুব ছোট শহর, তা নয়, আসানসোলের কথা ছেড়ে দিলে আর-পাঁচটা মহকুমা-সদরের তুলনায় মোটামুটি বড়ই বলতে হবে। রাস্তাঘাটে গাড়িঘোড়ার ভিড় লেগেই আছে। দোকানপাটও বেশ জমজমাট। তবু, কথা অনুযায়ী কাজ হলে ন’টার মধ্যে আমরা সেনেদের বাড়িতে পৌঁছে যেতে পারতুম। কিন্তু কথা অনুযায়ী কাজ হয়নি। ভাদুড়িমশাই কাল রাত্তিরে বলেছিলেন যে, ব্রেকফাস্ট সেরে সরাসরি আমরা এখানে চলে আসব। কিন্তু পরমেশবাবুর বাড়ি থেকে রওনা হবার পরই তার প্ল্যান পালটে যায়। পথের মধ্যে তিন জায়গায় তিনি গাড়ি থামান। প্রথমে একটা চশমার দোকানে ঢুকে হালকা মভ কালারের একজোড়া রোদ-চশমা কেনেন। তারপর থামেন আরও দু’জায়গায়। দুটোই নাকি তার পুরনো বন্ধুর বাড়ি। বললেন, অনেক দিন বাদে চন্দননগরে এসেছেন, আবার কবে আসা হবে তার ঠিক নেই, তাই এই সুযোগে বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎটা সেরে নিতে চান।
দুই বন্ধুর সঙ্গে কী কথা হয়েছিল, আমরা জানি না। তার কারণ, আমি ও সদানন্দবাবু গাড়ির মধ্যেই সারাক্ষণ বসে ছিলুম, দুটি বাড়ির কোনওটিতেই আমরা ঢুকিনি। তবে ভাদুড়িমশাইয়ের সঙ্গে তাদের নেহাত কুশল বিনিময় হয়ে থাকলে এক-একটা সাক্ষাৎকারে নিশ্চয় ঘণ্টা দেড়েক করে সময় লেগে যেত না। কথা শেষ হবার পর ভাদুড়িমশাইকে বিদায় জানাতে তারা যখন রাস্তায় নেমে আসেন, তখন অবশ্য এক পলকের জন্যে হলেও দু’জনকেই আমরা দেখেছি। দু’জনেরই বয়স মনে হল সত্তর-বাহাত্তর হবে। দ্বিতীয় বাড়ির বন্ধুটির একটা কথাও শুনেছি আমরা। কথাটা হল : “তা ধরো লাখ দশ-বারো তো হবেই। কিছু বেশিও হতে পারে।”
প্রথমে চশমা কেনা, তারপর দুই বন্ধুর সঙ্গে অতক্ষণ ধরে কথা বলা, ফলে সেনেদের বাড়িতে যেখানে ন’টার মধ্যে পৌঁছবার কথা, সেখানে বারোটারও একটু পরে আমরা পৌঁছই।
পৌঁছে আমি প্রথমটায় একটু অবাক হয়ে গিয়েছিলুম। পরক্ষণেই অবশ্য মনে হয় যে, এমনটা যে দেখব, তা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। বসতবাড়ির পাশের জমিতে মন্দির। জমির অন্য দিকে ছোট্ট একটি দোতলা বাড়ি। মাঝেখানের বাধানো বিশাল চত্বর জুড়ে মস্ত বড় ম্যারাপ খাটানো হয়েছে। এখন চলছে নকশাকাটা সাদা কাপড় দিয়ে বাঁশ ও তেরপলকে ঢাকা দেওয়ার কাজ। ডেকরেটরের লোকজন ছুটোছুটি করছে, বাঁশে পেরেক ঠোকার ঠকঠক শব্দ উঠছে সারাক্ষণ। তারই মধ্যে জনা তিন-চার লোক পায়জামা পাঞ্জাবি-পরা একজন বছর-পঁয়ত্রিশ বয়সের রোগামতন ভদ্রলোককে ঘিরে ধরে বলছে যে, এদের কাজ যদি না বিকেলের মধ্যে শেষ হয় তো তারা আলোর ব্যবস্থা করবে কখন?
আমরা গাড়ি থেকে নামতে ভদ্রলোক আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বললেন, “আপনারা?”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “আমরা কলকাতা থেকে আসছি। বিমলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।”
“ও, বুঝতে পেরেছি।” ভদ্রলোক বললেন, “আপনারা আমার সঙ্গে আসুন। মামাবাবু এখানেই ছিলেন, একটু আগে বাড়ি গেছেন। আসুন।”
বুঝলুম যে, এই হচ্ছে নুটু, অর্থাৎ বিমলভূষণের সেই ভাগ্নে। বাড়ি বলতে এ যে সেনেদের বসতবাড়ির কথা বোঝাচ্ছে, তাও বোঝা গেল।
মন্দিরপ্রাঙ্গণ থেকে বেরিয়ে একটা গেট পেরিয়ে বসতবাড়ির এলাকায় ঢুকে পড়া গেল। মস্ত বড় কম্পাউন্ডওয়ালা চুন-সুরকির সেকেলে বিশাল দোতলা বাড়ি। বিলিতি ম্যাগাজিনের ইলাসট্রেশনে ম্যানর হাউসের যে-সব ছবি দেখা যায়, এটিও দেখতে অনেকটা সেইরকম। কম্পাউন্ডের জমিতে অনায়াসেই বাগান করা চলত, কিন্তু সেসব করার কোনও চেষ্টা কখনও হয়েছে বলে মনে হয় না, সর্বত্র শুধু ঘাসই চোখে পড়ে। বাড়িটিও ল্যাপাপোঁছা ধরনের। তবে মেনটেন্যান্সে যে কোনও ত্রুটি নেই, সেটা বোঝ যায়। ত্রুটি ঘটলে এখানে-ওখানে ফাটল চোখে পড়ত। দেখা যেত যে, ফাটলের মধ্যে বট-অশথের চারা গজিয়ে গেছে। সে-সব চোখে পড়ল না। সদ্য বাড়িটির কলি ফেরান হয়েছে, তাও বুঝলুম। তবে, বাড়িটির আর্কিটেকচারাল প্যাটার্ন যতই না শ্রীহীন হোক, আয়তনে এটি এতই বিশাল যে, তাতেই খানিকটা সম্ভ্রমের উদয় হয়।
সামনের দরজাটিও বেশ বড়। টুর পিছন-পিছন ভিতরে ঢুকে দেখলুম, বেশ চওড়া একটি কাঠের সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। নটু অবশ্য দোতলায় উঠল না, আপনারা উপরে উঠে যান, মামাবাবু দোতলায় থাকেন বলে ডানদিকের একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। পর্দার আড়ালে-একটি তরুণী ও বাচ্চা একটি ছেলের মুখও চকিতে চোখে পড়ল আমার। সম্ভবত নুটুর বউ ও ছেলে।
আমরা দোতলায় উঠে ডোর-বেলের বোতাম টিপবার কয়েক সেকেন্ড বাদে যিনি এসে দরজা খুলে দিলেন, তাকে যেহেতু আগেই আমরা দেখেছি, তাই চিনতে অসুবিধে হল না। বিমলভূষণ আজ অবশ্য অন্য পোশাক পরেছেন। তার পরনে আজ সিল্কের পায়জামা ও পাঞ্জাবি। পায়ে শুড়-তোলা চটিজুতো। আমাদের দেখে যে একটু অবাক হয়েছে, তা তার চোখ দেখেই বোঝা গেল। বললেন, “আসুন, আসুন। কিন্তু আপনাদের তো কালই আসার কথা ছিল। এলেন না যে? কাজে আটকে গেসলেন?”
এর উত্তরে সত্য কথা বললে স্পষ্ট জানাতে হত যে, আমরা কালই এসেছি বটে, কিন্তু উঠেছিলুম অন্য জায়গায়। ভাদুড়িমশাই অবশ্য সত্যও বললেন না, মিথ্যে বললেন না। প্রশ্নটাকে বেমালুম এড়িয়ে গিয়ে বললেন, “চুরিটা আটকে দেওয়াই হচ্ছে আসল কথা। আশা করি, আটকে দিতে পারব। চলুন, আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করার আছে।”
বিমলভূষণের যেন হঠাৎই খেয়াল হল যে, আমাদের তখনও দরজায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে, বসতে বলা হয়নি। শশব্যস্ত হয়ে বললেন, “আরে কী কাণ্ড, আপনারা দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, আসুন, আসুন, ভিতরে এসে বসুন।”
দরজা পেরোলেই মস্ত ড্রয়িংরুম। এক দিকে একটি ডিভান। মাঝখানে বড়সড় সেন্টার টেবিল ঘিরে গোটা কয়েক শসোফা। দেওয়াল ঘেঁষে জানালার-তেলাঞ্চি-সমান-উঁচু টানা কাঁচের আলমারি। তাতে দেশি ও বিদেশি নানারকমের পুতুল সাজানো। অন্যদিকের দেওয়ালে পাশাপাশি তিনটি তেলরঙা পোর্ট্রেট। আমরা সেদিকে তাকিয়ে আছি দেখে বিমলভূষণ বললেন, “বাঁদিক থেকে আমার বাবা, ঠাকুর্দা আর ঠাকুর্দার বাবা।”
সদানন্দবাবু বললেন, “অর্থাৎ চন্দ্রভূষণ, কীর্তিভূষণ আর কালীভূষণ। ঠিক বলিচি?” বিমলভূষণ বললেন, “ঠিকই বলেছেন।…কিন্তু কলকাতা থেকে আপনারা স্নান সেরে বেরিয়েছেন তো? নাকি এখানেই স্নান করে নেবেন?”
“ও-সব সেরে তবেই রওনা হয়েছি।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “আপনি ব্যস্ত হবেন না। বরং কাজের কথা শুরু করা যাক।”
“কাজের কথা পরে হবে।” বিমলভূষণ হেসে বললেন, “অনেক বেলা হয়ে গেছে। আপনারা আগে খেয়ে নিন। আমরাও দুপুরের খাওয়া এখনও খাইনি। সবাই একসঙ্গে বসে খেয়ে নেব। কাজের কথা তার পরে হলেও ক্ষতি নেই। কথা সেরে তারপর গেস্ট হাউসে যাবেন। ওখানেই আপনাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।”
তা-ই হল। বিমলভূষণ ভিতরে চলে গিয়ে মিনিট দুই-তিন বাদে আবার ঘুরে এসে বললেন, “আপনারা আসুন। খেতে দেওয়া হচ্ছে। আমার স্ত্রী সবাইকে ডাইনিং রুমে নিয়ে যেতে বললেন।”
ডাইনিং রুমটি দোতলার একেবারে শেষ প্রান্তে। এটিও মস্ত বড় ঘর। মাঝখানে ওভাল ডাইনিং টেবিল। টেবিল ঘিরে খান দশেক হাই-ব্যান্ড চেয়ার।
পাশাপাশি তিনটি চেয়ারে বসে যাঁরা কথা বলছিলেন, আমরা গিয়ে ঘরে ঢুকতে তারা দাঁড়িয়ে উঠে নমস্কার করলেন। পরমেশ চৌধুরির কাছে এই সেন-পরিবারের একটা আন্দাজ কাল পেয়েছি, তাই খুব সহজেই এঁদের চিনে নেওয়া গেল। মহিলা দুটি বিমলভূষণের স্ত্রী ও কন্যা। তৃতীয়জন পুরুষ। সম্ভবত এ বাড়ির জামাতা। বিমলভূষণ পরিচয় করিয়ে দিলেন। দেখলুম, অনুমানে ভুল হয়নি। বিমলভূষণের স্ত্রী কনক প্রৌঢ়বয়সিনী। কিন্তু এক
পলক দেখলেই বোঝা যায় যে, এই মহিলা এককালে অসামান্য রকমের রূপবতী ছিলেন। সেই রূপের রেশ এখনও সম্পূর্ণ মিলিয়ে যায়নি, অস্তগামী সূর্যের রশ্মির মতো এখনও তার মুখেচোখে একটা মায়াজাল ছড়িয়ে রেখেছে। মেয়েটি তার মায়ের রূপ পায়নি। তার মুখে একটা অসন্তোষ ও অতৃপ্তির ভাবও দুর্লক্ষ্য নয়।
ঘরোয়া খাওয়া। ভাত, ডাল, দু’রকমের ভাজা, মাছ ও টক। সেই সঙ্গে শেষপাতে দই। খেতে-খেতে খুব একটা কথাও হল না। দেড়টার আগেই খাওয়ার পর্ব সমাধা হল। একটি ভূত এসে একটা মশলার বাটি এগিয়ে ধরল, তা থেকে এক চিমটি করে মশলা তুলে নিয়ে আমরা আবার বাইরের ঘরে এসে বসলুম।
ভাদুড়িমশাই বললেন, “কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করার আছে। কিন্তু আপনার তো এখন বিশ্রাম করার সময়, তাই না?”
বিমলভূষণ হেসে বললেন, “এই সময়ে একটু গড়িয়ে নিই ঠিকই, তবে ও নিয়ে ভাববেন না। কী বলবেন বলুন?”
“হিরে দুটো আপনি বলেছিলেন সিন্দুকে ভোলা থাকে। সিন্দুকটা কোথায়?”
“এই বাড়িতেই। আমার শোবার ঘরের দেওয়ালে-গাঁথা সিন্দুকে। তার চাবি থাকে আমার কাছেই।”
“সে দুটো একবার দেখা যায়?”
“তা কেন যাবে না? আপনারা একটু বসুন, আমি এখুনি নিয়ে আসছি।”
বিমলভূষণ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন মিনিট পাঁচেক বাদে। হাতে একটা ভেলভেটের বাক্স। আমাদের সামনে এসে বাক্সের ডালা খুলে ধরতেই চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। ভাদুড়িমশাই খুব মনোযোগ দিয়ে নিরীক্ষণ করলেন হিরে দুটিকে। তারপর বললেন, “ঠিক আছে, এবারে এ দুটিকে যথাস্থানে আবার রেখে আসুন।”
বাক্সের ডালা বন্ধ করে বিমলভূষণ আবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। এবং এবারেও ফিরে এলেন খানিক বাদেই। ফিরে এসে সোফায় বসে বললেন, “আর কী জানতে চান বলুন।”
“হরপার্বতীর চোখে ওই হিরে দুটো কাল কখন পরাবেন?”
“ভোর পাঁচটায়।” বিমলভূষণ বললেন, “তার আগে তো তোকজন আসা শুরুই হয় না।”
“হিরে দুটো যে সম্বচ্ছর আপনার শোবার ঘরের সিন্দুকে থাকে, আমি ধরেই নিচ্ছি যে, আপনার স্ত্রী আর মেয়ে-জামাই তা জানেন। কথা হচ্ছে আর-কেউ জানে কি না। এই ধরুন আপনার বাড়ির কাজের লোকেরা। তারা জানে?”
“জানে বলে মনে হয় না। বিমলভূষণ বললেন, “তবে হ্যাঁ, অনুমান তো করতেই পারে।”
“রাত্তিরে ওরা কোথায় থাকে?”
“এই বাড়িরই একতলায়। একতলার একদিকে ওরা থাকে আর অন্যদিকে থাকে আমার ভাগ্নে, নুটু।”
“হিরে দুটো যে সিন্দুকে থাকে, নুটু তা জানে?”
“মনে তো হয় না।” বিমলভূষণ বললেন, “ওকে বলেছি যে, হিরে থাকে ব্যাঙ্কের লকারে, চোত-সংক্রান্তির আগের দিন ব্যাঙ্কে গিয়ে লকার থেকে আমি বার করে আনি। আজও দশটা নাগাদ বাড়ি থেকে একবার বেরিয়েছিলাম। নুটুকে তখন বলে গিয়েছিলাম যে, ব্যাঙ্ক থেকে হিরে নিয়ে আসতে যাচ্ছি।”
শুনে, একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন ভাদুড়িমশাই। তারপর বললেন, “মাতা লুমিয়ের বলে কাউকে আপনি চেনেন?”
বিমলভূষণের মুখ দেখে মনে হল, এই প্রশ্নটার জন্যে তিনি তৈরি ছিলেন না। বললেন, “তাঁকে আপনারা চিনলেন কী করে?”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “আমরা চিনলাম কী করে, সেটা কোনও কথা নয়। আপনি চেনেন কি না বলুন।”
“চিনি।”
“কী করে চিনলেন? মানে সূত্রটা কী?”
“বলছি।” বিমলভূষণ বললেন, “আমার জামাই আদিত্যনাথ কলকাতার একটা এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোম্পানির ম্যানেজার। আপিসের কাজে গত ফেব্রুয়ারি মাসে ওকে ইউরোপে যেতে হয়। সেই সময়ে ফ্রান্সের ভিসা করাবার জন্যে ওকে একদিন কলকাতার ফ্রেঞ্চ কনস্যুলেটে যেতে হয়েছিল। আমি ওর সঙ্গে গিয়েছিলাম। তো সেইখানে মাতা লুমিয়েরের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ও গিয়েছিল ওর পাসপোর্টের মেয়াদ বাড়াতে। কথায় কথায় জানতে পারি যে, ও রিসার্চ-স্কলার, এ-দেশে এসেছে টেরাকোটার মন্দির নিয়ে কাজ করতে। আমি ওকে আমাদের মন্দিরের কথা জানাই। বলি যে, চোত-সংক্রান্তিতে আমাদের মন্দিরে খুব বড় একটা উৎসব হয়। ও সেই উৎসব দেখতে এসেছে।”
“এখানে এসে উঠেছে কোথায়?”
“এই বাড়িতেই উঠত।” বিমলভূষণ বললেন, “তবে কিনা সাহেব বলে কথা। ওদের হরেক রকম বায়নাক্কা। এদিকে আমরা তো সাহেবি কেতায় অভ্যস্ত নই। কে অত ঝক্কি পোয়াবে। তাই এই চন্নননগরেই আমাদের এক বন্ধুর বাড়িতে ওর থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আশা করছি, সেখানে ওর কোনও অসুবিধে হবে না। আজ সকালে ব্যাঙ্কে যাবার নাম করে যখন বেরোই তখন আসলে ওরই সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম।”
“এর আগে শেষ কবে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?”
উত্তর দেবার আগে এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন বিমলভূষণ। একটু ভেবে নিলেন। তারপর বললেন, “মনে পড়েছে। গত রবিবার। ওই যেদিন কলকাতায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাই। আপনার ওখান থেকে চলে আসছি, এমন সময় রাস্তায় একেবারে হঠাৎই ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। এয়ারপোর্টে কাকে যেন রিসিভ করতে যাচ্ছিল। পথে আমাকে দেখে গাড়ি থেকে নেমে পড়ে।”
“আপনাদের হিরের কথা ও জানে?”
“সে তো আমিই ওকে বলেছি। সেই হিরের চোখের হরপার্বতী দেখতেই তো ওর আসা। কাল ভোরেই ঠিক এখানে এসে যাবে।”
“এবারে শেষ প্রশ্নটা করি। নুটু লোকটি কেমন? ওকে আপনি কতটা বিশ্বাস করেন?”
“পুরোপুরি বিশ্বাস করি।” বিমলভূষণ বললেন, “না করে উপায় আছে? ওই তো সব সামলাচ্ছে।”
“বাস,” ভাদুড়িমশাই বললেন, “অনেকক্ষণ আপনাকে আটকে রেখেছি, এবারে আপনার ছুটি। সন্ধের দিকে একবার আসব। এখন যান, একটু গড়িয়ে নিন।
বিমলভূষণ সোফা থেকে উঠে দরজা পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিলেন। কাঠের সিঁড়ি দিয়ে আমরা নীচে নেমে এলুম। রওনা হলাম গেস্ট হাউসের দিকে।
গেস্ট হাউসের মুখে নুটুর সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন, “দোতলায় চলে যান, ওখানে আপনাদের জন্যে দুটো ঘর রেডি করে রেখেছি।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “আপনাদের পুজুরি ঠাকুরটির সঙ্গে একটু কথা বলব। তাকে পাওয়া যাবে?”
“নিশ্চয়ই যাবে।” নুটু বললেন, “নীচেই আছেন। আপনারা ঘরে যান, আমি তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।”
আমরা উপরে উঠে সিঁড়ির পাশের ঘরটা আমার ও সদানন্দবাবুর জন্য রেখে ধারের ঘরটা ভাদুড়িমশাইকে ছেড়ে দিলুম। গাড়ি থেকে আমাদের হ্যান্ডব্যাগ তিনটি উপরে তুলে দেওয়া হয়েছিল। জামাকাপড় পাল্টে ভাদুড়িমশাইয়ের ঘরে বসে সবে নিজেদের মধ্যে কথা বলতে শুরু করেছি, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল।
দরজা খুলে যাকে দেখা গেল, তার বয়স বছর তিরিশ-বত্রিশের বেশি হবে না। গৌরবর্ণ যুবা পুরুষ, পরনে গরদের ধুতি, ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত, গলায় ধবধবে সাদা উপবীত। নমস্কার করে বললেন, “আমার নাম শ্রীগৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য। আমিই এই মন্দিরের পূজারি। নুটুবাবু বললেন, আপনারা আমার সঙ্গে কথা বলতে চান।”
ঘরে একটিমাত্র চেয়ার। গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্যকে সেটায় বসতে বলে আমরা তিনজন খাটের উপরে বসলুম। ভাদুড়িমশাই কোনও ভণিতার মধ্যে না গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি এখানে কত দিন আছেন?”
“পাঁচ বছর।” গৌরাঙ্গ বললেন, “আগে আমার বাবা এখানে পূজো-পাঠ করতেন। তিনি অসুস্থ হয়ে দেশের বাড়িতে চলে যান। তখন থেকে আমিই এখানে কাজ করছি।”
“আপনাদের দেশ কোথায়?”
“বর্ধমান জেলার শক্তিগড়ে। সেখানে রেলগাড়ি থেকে নেমে মাইল পাঁচেক সাইকেল রিকশায় যেতে হয়। গ্রামের নাম বড় চণ্ডীপুর।”
ভাদুড়িমশাই একটা সিগারেট ধরালেন। দেশলাই কাঠিটা নিভিয়ে ঘরের মধ্যে অ্যাশট্রে না থাকায়, জানলা দিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করলেন। তারপর বললেন, “ভটচাজমশাই, আপনি কি নিত্য গঙ্গাস্নান করেন?”
গৌরাঙ্গ বললেন, “শরীর ভাল থাকলে নিত্যই করি। তবে শরীর তো নিত্য ভাল থাকে না। তখন এক-আধ দিন বাদ যায়।” জোড়া ভাদুড়ি-৪
ভাদুড়িমশাই আর কথা না বাড়িয়ে এবারে সরাসরি চলে এলেন হিরের প্রসঙ্গে। বললেন, “বিমলবাবু বলছিলেন যে, গঙ্গার ঘাটে দুজন লোককে আপনি হিরে নিয়ে বলাবলি করতে শুনেছিলেন। এটা কবেকার কথা?”
“গত মাসের মাঝামাঝির।” একটুক্ষণ চিন্তা করে গৌরাঙ্গ বললেন, “মার্চ মাসের চোদ্দো-পনেরো তারিখের।”
“তারা কী বলছিল।”
“বলছিল যে, ও-হিরে সেনেদের নয়, ওরা এক সায়েবের কাছ থেকে হাতিয়েছে, তাই চুরি করলে পাপ হবে না।”
“ঠিক এই কথাই আপনি বিমলভূষণকে বলেছিলেন?”
“আজ্ঞে না।” গৌরাঙ্গ সামান্য হাসলেন। বললেন, “ওভাবে কি বলা যায়? আমি শুধু বলেছিলাম যে, হিরে নিয়ে দু’জন লোককে কথা বলতে শুনেছি, তাই সাবধান হওয়া দরকার।”
“লোক দু’জন কোথাকার বলে মনে হয়?”
“তা তো জানি না। তবে চেহারা আমার মনে আছে। একজন ঢ্যাঙা, অন্যজন বেঁটে। দুজনেই কালো। বেঁটে লোকটার গালে একটা আঁচিল আছে। আবার দেখলে ঠিক চিনতে পারব।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “ঠিক আছে ভটচাজমশাই, আপনি যেতে পারেন।” গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য চলে গেলেন।
ভেবেছিলুম, জামাকাপড় পালটে ভাদুড়িমশাইও এবারে একটু বিশ্রাম করে নেবেন। কিন্তু তিনি জামাকাপড় পালটালেন না। দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, “আপনারা বিশ্রাম করুন, গাড়িটা নিয়ে আমি একটু বেরুচ্ছি। পাঁচটা নাগাদ ফিরব।”।
কোথায় কী কাজে তিনি বেরিয়ে গেলেন, তা জানি না, তবে ফিরে এলেন পাঁচটার মধ্যেই। আমি ও সদানন্দবাবু ইতিমধ্যে একটু ঘুমিয়ে নেবার চেষ্টা করেছি। তবে সদানন্দবাবুর ক্ষেত্রে চেষ্টাটা কিঞ্চিৎ সফল হলেও আমার ক্ষেত্রে একেবারেই হয়নি। ভাদুড়িমশাই ফিরে এসেই বললেন, “চলুন, স্ট্যান্ড থেকে এক চক্কর ঘুরে আসা যাক।”
যেতেই হয়েছিল। সেখানে পরমেশ চৌধুরির সঙ্গে দেখাও হয়ে গেল আবার। ভদ্রলোক একটা বেঞ্চিতে বসে তারই বয়সী জনা তিনেক বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিলেন। ভাদুড়িমশাইকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “তোমার কাজ কেমন এগোচ্ছে?” তাতে ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, “ভালই।” শুনে খুশি হলেন পরমেশ। বললেন, “কলকাতায় ফেরার আগে কিন্তু একটা দিন আমার বাড়িতে কাটিয়ে যেয়ো।”
স্ট্যান্ড থেকে ফিরতে-ফিরতে রাত হয়ে যায়। ফিরে সেনেদের মূল বাড়িতে যাই। সেখানে বিমলভূষণের সঙ্গে ভাদুড়িমশাইয়ের একান্তে কিছু কথা হয়। তারপর ওখানেই রাতের খাওয়া চুকিয়ে একটু আগে গেস্ট হাউসে ফিরেছি। ফিরে ভাদুড়িমশাইকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, বিমলভূষণের সঙ্গে তার কী কথা হল। তাতে তিনি হেসে বললেন, “কথা তো বিশেষ হয়নি। তবে হ্যাঁ, ওঁর শোবার ঘরে ঢুকে সিন্দুক খুলিয়ে ওই হিরেজোড়া আর একবার দেখে এলুম।” তারপর এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, “তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ুন। রাত জাগবেন না। কাল ভোর পাঁচটার আগেই নীচে নামতে হবে।”
কিন্তু শুয়ে পড়লেই কি ঘুম আসে? ডেকরেটরদের কাজ শেষ হয়নি। ইলেকট্রিক মিস্ত্রিরা সমানে চেঁচামেচি করছে। পেরেক ঠোকার শব্দেরও কামাই নেই। কেন যে ওরা শেষ মুহূর্তের জন্য সব কাজ ফেলে রাখে। এর মধ্যে ঘুমুনো সম্ভব?
অথচ, এত হই-হল্লা আর ঠকাঠক হাতুড়ি পেটার শব্দের মধ্যেও সদানন্দবাবু দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন। ভদ্রলোককে হিংসে হয়।
.
॥ ১০ ॥
আজ চোদ্দোই এপ্রিল, চৈত্র-সংক্রান্তি, বুধবার। ডেকরেটরের লোজন ও ইলেকট্রিক মিস্ত্রি-মজুরদের যে চিৎকার-চেঁচামেচি আর সেইসঙ্গে হাতুড়ি দিয়ে পেরেক ঠোকার যে অবিশ্রান্ত ঠকঠক শব্দের মধ্যে গতকাল শয্যাগ্রহণ করেছিলুম, রাত দুটো নাগাদ তা খানিকটা স্তিমিত হয়ে আসে। সম্ভবত সেই সময়ে আমার দুচোখের পাতা ঘুমে জড়িয়ে এসেছিল। কিন্তু খুব বেশিক্ষণ আমি ঘুমোতে পারিনি। খানিক বাদেই শঙ্খধ্বনি আর কাসর ঘণ্টার আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙে যায়। হাতঘড়ির রেডিয়াম লাগানো ডায়ালের দিকে তাকিয়ে দেখি, চারটে বাজে। সদানন্দবাবু তখনও ঘুমোচ্ছেন। তাকে আর জাগাই না। ঝটপট মুখ হাত ধুয়ে, দাড়ি কামিয়ে, স্নান সেরে নিই। তারপর তাকে ঠেলে তুলে দিয়ে জামাকাপড় পালটে নীচে নামতে নামতে সাড়ে চারটে বাজে। নীচে নেমে দেখি, ভাদুড়িমশাই আমার আগেই একতলায় এসে দাঁড়িয়ে আছেন।
তখনও রাত কাটেনি। অথচ এরই মধ্যে পিলপিল করে তোক আসতে শুরু করেছে। দেখতে দেখতে চত্বরটা ভরে গেল। তার মধ্যে বুড়ো, বুড়ি, যুবক, যুবতী তো আছেই, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েও কিছু কম নেই। কোলে বাচ্চা নিয়েও এসে গেছে অনেক মা। তারা চত্বরের শানে হাত ঠেকিয়ে সেই হাত তাদের কোলের বাচ্চার মাথায় ঠেকিয়ে দিচ্ছে। বাইরে থেকে ওদিকে লোক আসছে তো আসছেই। এ দেশে ধর্মের যে কী টান, আর সেই টানে মানুষ যে কীভাবে ছুটে আসে, এই শেষ রাত্তিরে এখানে এসে না দাঁড়ালে তা বুঝতেই পারতুম না।
মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। গেস্টহাউসের একতলার বারান্দাটা বেশ উঁচু। তাই এখানে দাঁড়িয়ে, জনতার মাথার উপর দিয়ে হরপার্বতীর মূর্তিটিকে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য বেশ উঁচু গলায় শিবস্তোত্র পাঠকরতে করতে একটি ঘণ্টা নেড়ে যাচ্ছেন। তাঁর দু’পাশে দুটি যুবাবয়সী মানুষ। একজন শাঁখ বাজাচ্ছে, অন্যজন কাসর। এইসব দেখছি ও শুনছি, এমন সময় দোতলা থেকে নেমে সদানন্দবাবু আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। বললুম, “স্নান করে নিয়েছেন?” তাতে তিনি বললেন, “তার সময় পেলুম কোতায়?…ওরে বাবা, এ তো দেকচি ইন্দ্রপুরীবানিয়ে ছেড়েছে।”
সদানন্দবাবু খুব একটা বাড়িয়ে বলেননি। চত্বরের উপরকার তেরপলের ছাউনির তলা দিয়ে তিন-চার ফুট অন্তর অন্তর আড়াআড়ি ভাবে টানা বাঁশের বাতা থেকে ঝোলানো অজস্র ইলেকট্রিক বালবের মালা থেকে অতিশয় কড়া আলো তো বিরিত হবে, সেই সঙ্গে ব্যবস্থা করা হয়েছে বেশ জোরালো দুটি ফ্লাড লাইটের। ফলে যেমন মন্দির তেমনি গোটা চরটিও আলোয় ঝলমল করছে। চত্বরটিকে ঘিরে জ্বলছে কিছু আমোর চরকিও। চন্দননগরের আলোর কারিগরদের সুখ্যাতির কথা কে না জানে। সুযোগটা যখন নিজেদের এলাকাতেই পাওয়া গেছে, তখন অন্তত খানিকটা কেরামতি না দেখিয়ে তারা ছাড়বে কেন। এতক্ষণ যে হট্টগোল চলছিল, হঠাৎই যেন তার মাত্রা আরও বেড়ে গেল। সামনে তাকিয়ে দেখলাম, ভলান্টিয়ার ছেলেরা চত্বরের ভিড়কে দু’পাশে খানিকটা ঠেলে দিয়ে মাঝ বরাবর একটা রাস্তা করে দিচ্ছে। কেন এমন করা হচ্ছে, জিজ্ঞেস করার জন্য ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে তাকাতে তিনি চাপা গলায় বললেন, “পিছনে তাকিয়ে দেখুন।”
ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখলুম, সেনেদের বসতবাড়ির দিক থেকে ছোট্ট একটি মিছিল ধীরে ধীরে চত্বরে এসে ঢুকল। মিছিলের সামনে বিমলভূষণ। তার পিছনে পরপর তার স্ত্রী, জামাতা ও কন্যা। তারও পিছনে আট-দশ বছরের দুটি ছেলে, এবং সর্বশেষে একটি অল্পবয়সী বউ। বউটিকে দেখে চকিতে মনে হল, আগেও কোথাও একে দেখেছি। কিন্তু ঠিক যে কোথায় দেখেছি, তক্ষুনি তা মনে করতে পারলুম না। মিছিলের সামান্য পিছনে মাতা লুমিয়েরকেও দেখলুম। দেখেই বুকটা ছ্যাত করে উঠল। লোকটা কি সত্যিই মন্দিরের এই উৎসব দেখতে এসেছে? নাকি অন্য কোনও মতলব আছে ওর?
নুটু চত্বরের মধ্যেই ছিল। সেনেদের বাড়ির মিছিল চত্বরে এসে পৌঁছবামাত্র ভিড় ঠেলে সেইদিকে এগিয়ে গেল সে। শাঁখ, কাঁসর ও ঘন্টার শব্দ একটুক্ষণের জন্য থেমে ছিল, এবারে আবার ঘন ঘন শঙ্খধ্বনি হতে লাগল, কাসর-ঘণ্টা দ্বিগুণ উৎসাহে বাজতে থাকল, আর গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্যও তার গলা আরও উঁচুতে উঠিয়ে মন্ত্রপাঠ শুরু করলেন।
বিমলভূষণ আজ সাদা গরদের ধুতি পরেছেন। গলার দু’দিক দিয়ে জরির পাড় বসানো। গরদের চাদর ঝুলছে। কপালে শ্বেতচন্দনের ফোঁটা। জুতো পরেননি। পা দুটি অনাবৃত। দু’হাতে ধরে আছেন সেই ভেলভেটে মোড়া বাক্সটিকে, যেটিকে কাল দুপুরে ওঁর বাড়িতে আমরা দেখেছি, আর যে বাক্সের মধ্যে মহার্ঘ সেই হিরে দুটি রয়েছে বলে আমি জানি।
ভিড়ের ভিতর দিয়ে সরু যে পথ করে দেওয়া হয়েছিল, সেনেদের বাড়ির মিছিল সামনে এগিয়ে গেল সেই পথ দিয়ে। তারপর একে একে সবাই মন্দিরের বারান্দায় উঠে পড়লেন। মাতা লুমিয়ের অবশ্য আর এগোল না। হাতে ক্যামেরা নিয়ে সে মন্দিরের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে রইল। বিগ্রহের অক্ষিকোটরে হিরে দুটি বসিয়ে দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই সে তার ছবি তুলবে, ক্যামেরার লেন্সে চোখ রেখে তার দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখেই তা বুঝতে পারলুম।
গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য এই মুহূর্তটির জন্য একেবারে তৈরি হয়েই ছিলেন। হাতে একটি মার পাত্র নিয়ে তিনি বিমলভূষণের সামনে এসে দাঁড়ালেন। মন্ত্রোচ্চারণ করে তার কপালে আর-এক প্রন্ত চন্দন লেপে দিলেন। মাথায় ধানদুর্বা রাখলেন, সর্বাঙ্গে গঙ্গাজল ছেটালেন। তারপর সরে এলেন তার সামনে থেকে। বারান্দা থেকে মন্দিরের ভিতরে ঢুকে গেলেন বিমলভূষণ।
সবই এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি। ভেলভেটের বাক্স খুলে হরপার্বতীর তৃতীয় নয়নে হিরে দুটি পরিয়ে দেওয়ার দৃশ্যও স্পষ্ট দেখলম। কাঁসর-ঘণ্টা সমানে বাজছে ঘন ঘন শধ্বনি হচ্ছে, জনতা সোনাসে চিৎকার করছে–জয় শঙ্কর, জয় পার্বতী। ওদিকে মাতা লুমিয়েরের ক্যামেরার ফ্ল্যাশ বা ঝলসে উঠছে বারবার। তারই মধ্যে দেখলুম, হরপার্বতীর যুগলমূর্তিকে জোড়হস্তে নমস্কার করে বিমলভূষণ খুবই ধীর পায়ে মন্দিরের ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসছেন।
বিমলভূষণ বেরিয়ে আসার পর তার পরিবারের লোকেরা মন্দিরের মধ্যে ঢুকে বিগ্রহের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁদেরই বাড়ির অনুষ্ঠান, সুতরাং মন্দিরে ঢোকার অগ্রাধিকারও তাদেরই।
ঠিক এই সময়েই ঘটল একটি ভয়াবহ ঘটনা। মন্দির, চত্বর ও গেস্ট হাউসের একতলা-দোতলার সমস্ত আলো একেবারে একই সঙ্গে নিভে গেল। লোকজনেরা ছুটোছুটি শুরু করে দিল, বাচ্চারা তারস্বরে কাঁদতে লাগল, ভলান্টিয়াররা চেঁচিয়ে বলতে লাগল, “আপনারা ভয় পাবেন না, ছুটোছুটি করবেন না, যে যেখানে আছেন সেইখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকুন, আমরা জেনারেটর চালাবার লোক আনতে পাঠিয়েছি, সে এসে পড়লেই জেনারেটর চালু হয়ে যাবে।”
আমার ভয় হল, এক্ষুনি একটা স্ট্যাম্পিড শুরু হয়ে যেতে পারে। ভোর হয়েছে, সূর্য উঠেছে, চারদিকে আলো ফুটেছে, অথচ মাথার উপরে তেরপলের ছাউনি থাকায় আর টিন ও চট দিয়ে চারপাশ ঘিরে রাখায় এই চত্বরের মধ্যে এক ফোঁটাও দিনের আলো ঢুকতে পারছে না। চারদিকে একেবারে জমাট অন্ধকার। এর মধ্যে যদি স্ট্যাম্পিড শুরু হয় তো আর দেখতে হবে না, বিস্তর লোকের হাত-পা ভাঙবে, এক-আধটা বাচ্চাও হয়তো ভিড়ের চাপে পিষে গিয়ে মারা পড়তে পারে।
জেনারেটর অবশ্য পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চালু হয়ে গেল। ফটাফট আলো জ্বলে উঠল আবার। আর আলো জ্বলতেই গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্য আর্তনাদ করে উঠলেন : “আরে, হরপার্বতীর হিরে কোথায় গেল!”
বিমলভূষণ তার পরিবারের লোকদের সঙ্গে মন্দিরের বাইরের বারান্দায় সামনের দিকে তাকিয়ে, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মনে হল, অন্যেরা যখন ছোটাছুটি করছিল, তখন তিনি বারান্দা থেকে নীচে নামেননি। গৌরাঙ্গ ভট্টাচার্যের আর্তনাদ শুনে তিনি মন্দিরের দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন, তারপর চকিতে ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে, বারান্দা থেকে নেমে, প্রায় দৌড়ে চলে এলেন আমাদের কাছে। এসেই, ভাদুড়িমশাইয়ের হাত ধরে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বললেন, “এ কী হল মিঃ ভাদুড়ি?”
ভাদুড়িমশাই শান্ত গলায় বললেন, “ধৈর্য ধরুন, উতলা হবেন না। আমার ধারণা, লোডশেডিং হয়নি, মেন সুইচটা কেউ অফ করে দিয়েছে। আপনি সেটা চাল করার ব্যবস্থা করুন।”
“কিন্তু হিরে দুটোর কী হবে?”
“হিরে আপনি ফেরত পাবেন।” ভাদুড়িমশাই সেই একই রকমের শান্ত গলায় বললেন, “এখন যা বলছি, সেই কাজটা করুন তো।”
বলে আর তিনি দাঁড়ালেন না। গেস্ট হাউসের বারান্দা থেকে নেমে, চত্বর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে চাপা গলায় আমাকে বললেন, “সদানন্দবাবুকে নিয়ে আমার সঙ্গে আসুন।”
বিনা বাক্যে আমরা তার সঙ্গ নিলুম। বুঝলুম যে, এখন কোনও প্রশ্ন করে লাভ নেই। প্রশ্ন করলেও জবাব পাওয়া যাবে না। লম্বা লম্বা পা ফেলে মন্দির প্রাঙ্গণ পেরিয়ে গেলেন ভাদুড়িমশাই, সেনেদের কম্পাউন্ড ওয়ালের গেট দিয়ে ঢুকে তাদের বসতবাড়ির পথ ধরলেন। এত জোরে তিনি হাঁটছিলেন যে, তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে আমাদের বেশ কই হচ্ছিল। পিছন থেকে তবু বললুম, “ও বাড়িতে গিয়ে কী হবে? বিমলভূষণরা তো কেউ বাড়িতে নেই, ওরা তো মন্দিরে।”
ভাদুড়িমশাই আমার কথার কোনও জবাব দিলেন না। বসতবাড়ির সদর দরজা খোলাই ছিল, তিনি ভিতরে ঢুকে, দোতলার সিঁড়ির দিকে না গিয়ে, একতলারই ডানদিকের ঘরের দরজার কড়া ধরে জোরে-জোরে নাড়তে লাগলেন।
মিনিট খানেক ধরে ক্রমাগত কড়া নাড়ার পর যে বউটি এসে দরজা খুলে দিল, আজই কিছুক্ষণ আগে বিমলভূষণদের মিছিলের শেষে তাকে আমি দেখেছি। দেখে মনে হয়েছিল, আগেও কোথাও একে আমি দেখেছিলুম, কিন্তু ঠিক কোথায় যে দেখেছি, সেই মুহূর্তে তা মনে পড়েনি। এখন মনে পড়ল যে, কাল দুপুরে নুটু যখন আমাদের এই বাড়িতে নিয়ে এসে, দোতলার সিঁড়িটা দেখিয়ে দিয়ে একতলার এই ঘরে ঢুকে যায়, তখন পর্দার আড়ালে এরই মুখ আমি চকিতে একবার দেখতে পেয়েছিলুম।
বউটির মুখে ভয়ের ছাপ। দরজা খুলে আমাদের দেখে মুখ নামিয়ে স্বলিত গলায় জিজ্ঞেস করল, “আপনারা?”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “আমরা কলকাতা থেকে এসেছি।”
“কিন্তু আমার স্বামী তো এখন বাড়িতে নেই।”
“আমরা আপনার স্বামীর কাছে আসিনি।” ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, “আমরা আপনার কাছেই এসেছি। চটপট হিরে দুটো বার করে দিন। কথা দিচ্ছি, কেউ কিছু জানবে না।”
মুখ তুলে ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে তাকাল বউটি। কী দেখল, সেই জানে। তারপর আর কথা না বাড়িয়ে, ব্লাউজের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে ছোট্ট একটা কাগজের পুরিয়া বার করে এনে সেটা ভাদুড়িমশাইয়ের হাতে তুলে দিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে বলল, “আমার স্বামীকে আমি বাঁচাতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারলাম না।”
“বাঁচাতে হবে কেন,” ভাদুড়িমশাই বললেন, “আর তা ছাড়া, এই হিরে দিয়ে বাঁচানো যায়? এ তো নকল হিরে!”
বলে আর দাঁড়ালেন না। বসতবাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের নিয়ে ফের মন্দিরের দিকে রওনা হলেন।
.
॥ ১১ ॥
মন্দিরে যখন ফিরে যাই, জেনারেটরের ঘটঘট শব্দ তখন বন্ধ হয়ে গেছে। মেন সুইচটা সত্যিই কেউ অফ করে দিয়েছিল। সেটা ফের অন্ করে দেওয়ায় ফিরে এসেছে আসল আলো। চত্বর ছেড়ে যারা চলে গিয়েছিল, তারাও আবার ফিরে এসেছে। আবার জমে উঠেছে ভিড়। হরপার্বতীর হিরে যে পাওয়া গেছে, আর নতুন করে পরিয়েও দেওয়া হয়েছে বিগ্রহের চোখে, এই খবর রটে যাওয়ায় ভিড় ক্রমে আরও বেড়ে চলেছে। কিন্তু সেই ভিড়ের মধ্যে মাতা লুমিয়েরকে দেখতে পেলুম না। বিমলভূষণকে এই নিয়ে প্রশ্ন করতে তিনি বললেন, “সে তো তার দেশের কোন কাগজে ছাপবে বলে ছবি তুলতে এসেছিল। নতুন করে ওই যে আবার বিগ্রহের চোখে হিরে দুটো পরিয়ে দিলুম, তার ছবি তুলে নিয়ে সে আর দাঁড়ায়নি, ক্যামেরা নিয়ে চলে গেছে।”
এরপরে আর মন্দিরে আমরা খুব বেশিক্ষণ থাকিনি। থাকার কোনও দরকারও ছিল না। বিমলভূষণের পরিবারের লোকেরা খানিক আগেই বসতবাড়িতে ফিরে গেছেন। ভাদুড়িমশাই বললেন, “একটু চা পেলে ভাল হত।” শুনে বিমলভূষণ বললেন, “চলুন, বাড়িতে গিয়ে চা খাব।”
এখন আমরা বিমলভূষণদের দোতলার ড্রয়িংরুমে বসে চা খাচ্ছি। চা খেতে-খেতেই বিমলভূষণ বললেন, “যাক, আর হিরে চুরি যাবার ভয় নেই। মন্দিরে দুজন পাহারাদার বসিয়ে রেখে এসেছি। সারাক্ষণ-তারা হরপার্বতীর উপরে নজর রাখবে।”
ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, “কিন্তু ও দুটো তো আসল হিরে নয়।”
চা খেতে-খেতেই বিষম খেলেন বিমলভূষণ। তারপর কোনওক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে তোতলাতে-তোতলাতে বললেন, “তা তার মানে?”
‘মানে খুবই সহজ।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “কিন্তু একটা প্রশ্ন করি। আপনি কি হিরের আসল-নকল বোঝেন?”
“তা কেন বুঝব না খুব ভালই বুঝি।” উত্তেজিত গলায় বিমলভূষণ বললেন, “এটাও বুঝি যে, আমাদের বিগ্রহেব হিরে দুটি একেবারে হানড্রেড পারসেন্ট জেনুইন।”
সদানন্দবাবু বললেন, “টু হানড্রেড পারসেন্ট। সে তো আমি কাল দুপুরে যখন দেকলুম, তখনই বুজিচি! কী জেল্লা।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “আপনারা দুজনেই কারেক্ট। যে হিরে কাল দুপুরে আমরা দেখেছিলুম, সত্যিই তা মোলো-আন খাঁটি। কিন্তু…”।
বিমলভূষণ বললেন, “এর মধ্যে আবার কিন্তু আসছে কোত্থেকে?”
“আসছে আসছে। তাব কারণ, আজ যে হিরে পরানো হয়, পরাবার পরে চুরি যায়, আর তারপরে আমি উদ্ধার করে আনি, আর তারও পরে আবার বিগ্রহের চোখে বিমলভূষণ যা নতুন করে পরিয়ে দেন, তা কিন্তু সেই কালকের হিরে নয়, স্রেফ নকল।”
“বলেন কী, ও দুটো নকল হিরে? আর আমি তা বুঝতে পারলুম না?”
“শুধু আপনি কেন, কেউই বুঝতে পারেনি।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “পারার কথাও নয়। একে তো ওই হট্টগোল, তার উপরে ফ্লাডলাইট জ্বলছে, আলোর চর্কি ঘুরছে, একেবারে ধাঁধা লাগিয়ে দেওয়া ব্যাপার। তার মধ্যে কে বুঝবে যে, ও দুটো হিরে নয়, কাঁচ? বোঝা সম্ভব?”
“কিন্তু আমি তো সিন্দুক থেকেই ভেলভেটের বাক্স বার করে নিয়ে মন্দিরে গিসলুম। সেই বাক্স থেকে বার করেই তো বিগ্রহের চোখে হিরে দুটো বসিয়ে দিই!”
“বিমলবাবু, আপনার ওই বাক্সটাই জেনুইন, হিরে দুটো নয়।”
“বাক্সের ভিতর থেকে জেনুইন হিরে দুটো ল হলে কে নিল? কখন নিল?”
পট থেকে নিজের পেয়ালায় আবার নতুন করে লিকার ঢেলে নিলেন ভাদুড়িমশাই। তাতে দুধ-চিনি মিশিয়ে চামচ দিয়ে নেড়ে নিলেন। তারপর এক চুমুক চা খেয়ে পেয়ালাটাকে পিরিচে নামিয়ে রেখে বললেন, “কে নিয়েছে, তাও বুঝতে পারেননি। অবিশ্যি পারবেনই বা কী করে? গোয়েন্দা নিজেই যে হিরে চুরি করতে পারে, তা তো আপনার জানার কথা নয়।”
“তার মানে?”
“তার মানে হিরেজোড়া তো প্রথম দেখি কাল দুপুরে। তারপর কাল রাত্তিরে আপনার শোবার ঘরে গিয়ে আপনাকে দিয়ে সিন্দুক খুলিয়ে হিরে দুটোকে যখন দ্বিতীয়বার দেখি, তখনই আপনার ভেলভেটের বাক্স থেকে ও দুটি সরিয়ে নিয়ে তার জায়গায় দুটো নকল হিরে রেখে দিই। কাজটা করেছিলুম মাত্র এক লহমার জন্যে আপনার দিকে পিছন ফিরে। আপনি টেরও পাননি।”
দেখলুম, যেমন বিমলভূষণের, তেমনই সদানন্দবাবুরও চোয়াল ঝুলে পড়েছে। বিমলভূষণ অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, “অ্যাঁ?”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “হ্যাঁ। এই নিন আপনার আসল হিরে।”
পকেটে হাত দিয়ে ছোট্ট একটা এনভেলাপ বার করে তিনি বিমলভূষণের দিকে এগিয়ে দিলেন। বিমলভূষণ খাম খুলে জিনিস দুটি বার করতেই তা ঝকমক করে উঠল।
বেশ কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে হিরে দুটির দিকে তাকিয়ে রইলেন বিমলভূষণ। তারপর তার হতভম্ব ভাবটা কেটে যেতে মুখ তুলে ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, “কিন্তু….কিন্তু এই হিরেজোড়া আপনি সরিয়েছিলেন কেন?”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “ও দুটো আগে আপনার সিন্দুকে তুলে রেখে আসুন, অন্য কথা তারপরে হবে। যান।”
বিমলভূষণ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন মিনিট তিন-চার বাদে। তারপর ফের সেই প্রশ্ন তুললেন। “এবারে বলুন সরিয়েছিলেন কেন? আপনি কি জানতেন যে, বিগ্রহের চোখ থেকে ও-দুটো আজ চুরি হবে?”
“জানতুম বললে বাড়িয়ে বলা হবে।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “আসলে যে-কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তি এসব ক্ষেত্রে যা করে থাকে, আমিও তা-ই করেছিলুম। অর্থাৎ আশঙ্কা করেছিলুম। তা আশঙ্কা তো আপনারও ছিল বিমলবাবু। তা যদি না-ই থাকবে তো আপনি আমার কাছে ছুটে গিয়েছিলেন কেন? সে তো চুরিটা আমি ঠেকিয়ে দেব, এই ভরসাতেই। তাই না?”
একটুক্ষণের জন্যে চুপ করে রইলেন ভাদুড়িমশাই। তারপর বললেন, “আপনার সঙ্গে আমার অবশ্য একটা তফাত আছে। সেটা এই যে, আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও হরপার্বতীর চোখে আপনি আসল হিরেই পরাবার কথা ভেবেছিলেন। আমি সে-ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা করেছিলাম যে, আসল হিরে আপনি পরাতেই পারেননি। আশা করি, অন্তত এখন আপনি বুঝতে পারছেন, আমি ঠিক কাজই করেছিলুম।”
“তা তো করেইছিলেন।” বিমলভূষণ বললেন, “কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না। এত তাড়াতাড়ি আপনি ওই নকল…মানে কাঁচের চোখ জোগাড় করলেন কী করে? দেখতে তো হুবহু একই রকম!”
ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, “ও-সব আমাদের ট্রেড সিক্রেট। আপনার আসল হিরেজোড়া যে খোয়া যায়নি, তাতেই আপনি খুশি থাকুন। আর হ্যাঁ, চুরি তো গিয়েছিল নকল হিরে। কীভাবে, কার কাছ থেকে তা আমি উদ্ধার করলুম, দয়া করে তা নিয়েও কোনও প্রশ্ন করবেন না।”
.
॥ ১২ ॥
সেনেদের বাড়িতে চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে মাছ-মাংস খাওয়া হয় না। ধাতব কিংবা চিনামাটির থালাবাসনও ব্যবহার করা হয় না। দ্বিপ্রহরিক আহার্য কলার পাতায় পরিবেশন করা হল। আহার্য বলতে আতপ চালের ভাত, মুগের ডাল, দুতিন রকমের ভাজাভুজি, ধোঁকা ও ছানার দালনা, দই ও সন্দেশ। খাবার জল দেওয়া হল মাটির গেলাসে। খেয়ে বেশ তৃপ্তি পাওয়া গেল।
ভাদুড়িমশাইয়ের হাতে শুধু একটা পারিশ্রমিকের খাম ধরিয়ে দিয়েই বিমলভূষণ ক্ষান্ত থাকেননি। বারবার অনুরোধ করেছিলেন যে, রাতটাও যেন আমরা তার ওখানে কাটিয়ে আসি। কিন্তু ভাদুড়িমশাই কিছুতেই রাজি হলেন না। বললেন, “আজও আমরা চন্দননগরে থাকব ঠিকই, তবে এখানেই আমার এক পুরনো বন্ধুকে কথা দিয়েছি যে, বিকেল আর রাতটা তার সঙ্গে কাটাব। কিন্তু যাবার আগে একটা কথা বলে যাই, হিরে দুটো ইনসিওর করে ফেলুন। এ নিয়ে আর গড়িমসি করবেন না।”
নীচে নেমে আমরা গাড়িতে উঠে পড়লুম। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ভাদুড়িমশাই বললেন, “নুটু বোধহয় পরমেশের বাড়িতে এতক্ষণে পৌঁছে গেছে।”
শুনে আমি অবাক। বললুম, “জানলেন কী করে?”
“খাওয়ার ডাক পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে যে আমি ডাইনিং হলে যাইনি, গিয়েছিলাম আপনাদের একটু পরে, সেটা লক্ষ করেছিলেন?”
“তা করেছিলুম। ড্রয়িং রুমে বসে আবার একটা সিগারেট ধরিয়েছিলেন বুঝি?”
“না,” ভাদডিমশাই বললেন, “বিমলভূষণের সঙ্গে আপনাদের খেতে রওনা করিয়ে দিয়ে চটপট নীচে নেমে একবার নুটুদের ঘরে যাই। আশা করেছিলুম, নুটুর সঙ্গে দেখা হবে। হলও। তার বউয়ের কাছে নুটু সব শুনেছে। বলল যে, বউ যে এ কাজ করবে, সে তা জানত না। আমি বললুম, খেয়ে আমরা পরমেশ চৌধুরির বাড়িতে চলে যাব, সে যেন সেখানে গিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করে। পরমেশকে নুটু চেনে, বাড়ি চিনতে কোনও অসুবিধে হবে না। এতক্ষণে পৌঁছে গিয়ে থাকবে।”
সত্যিই তা-ই। নটু সত্যিই পরমেশবাবুর বৈঠকখানায় বসে অপেক্ষা করছিল। আমরা গিয়ে ঢুকতেই সে চেয়ার থেকে উঠে এসে ভাদুড়িমশাইয়ের পা জড়িয়ে ধরে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। তারপর নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলল, “আমার বউ যা করেছে, আমার কথা ভেবেই করেছে। কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি এর বিন্দুবিসর্গও জানতুম না। আপনি যদি সব কথা শোনেন…”
নুটুর কথা শেষ হল না। ভাদুড়িমশাই তাকে বাধা দিয়ে বললেন, “মোটামুটি সবই আমি জানি। এখন যদি বেচে দেন, তা হলে লোকসানের অঙ্কটা কীরকম দাঁড়াবে?”
“তা প্রায় দশ-বারো লাখ।”
“তা হলে এখন বিক্রি করবেন না। এতদিন যখন ধরে রেখেছেন, তখন আরও কিছুদিন ধরে রাখুন।
“তা হলে এখন যে দাম পাচ্ছি, দেরি করলে তো তাও পাব না। বাজার খারাপ।”
“এখা খারাপ। কিন্তু এই অবস্থা তো চলতে পারে না। পরে নিশ্চয়ই ঘুরবে। নার্ভ শক্ত রাখুন, ভেঙে পড়বেন না।”
“কিন্তু ইতিমধ্যে যদি…”
“জানাজানি হয়ে যায়?” ভাদুড়িমশাই মৃদু হেসে বললেন, “আমি কথা দিচ্ছি, কাউকে জানাব না।”
ভাদুড়িমশাইয়ের মুখের দিকে তাকাল নটু। কয়েক মুহূর্তের জন্য তাকিয়েই রইল। তারপর চোখ নামিয়ে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।
বাইরে থেকে একটা ভটভট শব্দ ভেসে এল। বুঝলুম যে, নুটু এখানে মোটরবাইকে করে এসেছিল, এখন আবার ফিরে যাচ্ছে। শব্দটা মিলিয়ে যাবার পরে ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে সদানন্দবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “কী ব্যাপার বলুন দিকি? হতে পারে নকল হিরে, কিন্তু এই যে সেটা চুরি হল, আর আপনি সেটা উদ্ধার করে দিলেন, এর মধ্যে নো ফ্রেঞ্চ কানেকশন?”
ভাদুড়িমশাই একটা সিগারেট ধরালেন। এক মুখ ধোয়া ছাড়লেন। তারপর সেই আগের মতোই মৃদু হেসে বললেন, “ভেবেছিলাম একটু গড়িয়ে নেব, কিন্তু আপনার ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে, সবকিছু না-জানলে আপনার পেটের ভাত হজম হবে না।..না, এর মধ্যে কোনও ফ্রেঞ্চ কানেকশন নেই।”
“তার মানে লুই আঁতোয়ান ওই যে টাকা চেয়ে চিঠি লিখেছিল?”
“টাকা তাকে দেবে কে? চন্দ্রভূষণ? তিনি তো চিঠিতে কী আছে, তা জানতেও পারেননি। তার আগেই তিনি জ্বরে পড়েন। মারাও যান সেই জ্বরেই।”
বললুম, “কিন্তু টাকা না-পেয়ে ব্যাপারটাকে লুই আর পার্স করেনি?”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “মনে তো হয় না। আমার ধারণা, ধার শোধ করতে না-পারায় লোকটার জেল হয়, আর জেলের মধ্যেই সে মারা যায়। অবশ্য এটা আমার ধারণা মাত্র, ঠিক কী যে হয়েছিল, তা তো জানার উপায় নেই। তবে হ্যাঁ, আর-কোনও চিঠি সে বোধহয় লেখেনি। লিখলে সেকথা বিমলভূষণ নিশ্চয় জানাত।”
“আর ওই মার্ত্যাঁ লুমিয়ের?”
“ও তত নেহাতই একজন রিসার্চ স্কলার। হিন্দু টেম্পল নিয়ে রিসার্চ করতে এসেছে, কাজ শেষ করে দেশে ফিরে যাবে।…না না, চুরি-বাটপাড়ির সঙ্গে ওর কোনও সম্পর্ক নেই।”
আমার সন্দেহ কাটছিল না। বললুম, “কৌশিক ওকে প্রথমবার দেখে বলেছিল, লোকটার চোখ নীল। পরে আমি শ্রীরামপুর পেরিয়ে দেখলুম নীল নয়, বাদামি। এটা কী করে হয়?”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “হতেই পারে। কনটাক্ট লেন্স পালটালেই হয়। আজকাল তো ওটাই ফ্যাশন।”
পরমেশ চৌধুরি ইতিমধ্যে বাড়ির ভিতরে গিয়ে চায়ের কথা বলে এসেছিলেন। ভৃত্য এসে সেন্টার টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম সাজিয়ে দিয়ে গেল। সদানন্দবাবু নিজের পেয়ালায় লিকার ঢেলে নিলেন। অন্যেরা যিনি যেমন পছন্দ করেন, সেইমতোবানিয়েও দিলেন অন্যদের চা। তারপরে নিজের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে বললেন, “একটা কব্জিজ্ঞেসকরব?”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “মাত্র একটা কেন, যে কটা খুশি।”
“গতকাল সকালে এখান থেকে রওনা হয়ে, সরাসরি সেনেদের বাড়িতে না গিয়ে, তিন জায়গায় আমরা থেমেছিলুম। প্রথমে একটা চশমার দোকান থেকে আপনি একজোড়া সান- গ্লাস কেনেন। ওটা কেনার কি তখনই খুব দরকার ছিল?”
“ছিল বই কী।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “কলকাতা থেকে নিয়ে আসিনি, তাই কিনতে হল। সানগ্লাসের মত্ত সুবিধে। ওটা পরলে আপনি সবাইকে দেখতে পান, কিন্তু আপনার চোখ কেউ দেখতে পায় না। ফলে কেউ বুঝতে পারে না যে, ঠিক কোন দিকে আপনি তাকিয়ে আছেন বা ঠিক কার উপরে নজর রাখছেন।”
“বুঝলুম। কিন্তু তারপরই দুই বন্ধুর বাড়িতেও আপনি গেছলেন। তারা কে?”
“আপনার আগের প্রশ্নটা ভাল ছিল। এটাও বেশ ভাল।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “প্রথম জনের নাম আদিনাথ ঘোয় আর দ্বিতীয় জনের নাম শ্ৰীমন্ত বসাক।…ওহে পরমেশ, তোমরা তো এখানকার পুরনো বাসিন্দা, এঁদের চেনো না?”
“কেন চিনব না?” পরমেশ বললেন, “ওঁরা দুজনেই তো স্ট্র্যান্ডে প্রায়ই হাঁটতে আসেন।”
“ওঁরা কী করেন, তাও জানো আশা করি?”
“জানি বই কী। আদিনাথবাবু শেয়ার মার্কেটের ব্রোকারি করতেন। কলকাতায় ওঁদের ছোটখাটো একটা আপিসও আছে। তবে আজকাল আর উনি বেচাকেনার কাজটা নিজে করেন না। কলকাতার আপিসের কাজকর্মও ওঁর ছেলেই দেখছে। ভদ্রলোকের শেয়ারের জ্ঞান শুনেছি টাটনে। এও শুনেছি যে, আদিনাথবাবু কাজকর্ম থেকে অবসর নিলে কী হয়, কোন শেয়ারটা কেনা ঠিক হবে আর কোনটা হবে না, সেটা বোঝার জন্য এখনও অনেকেই ওঁর কাছে যায়।”
“কারেক্ট। আর শ্ৰীমন্ত বসাক?”
“উনি এখানকার একজন নামজাদা জুয়েলার।” পরমেশ বললেন, “গয়নার ব্যাবসা ছাড়া নানা রকমের প্রেস স্টোনের একটা সাইড বিজনেসও আছে বলে শুনেছি।”
“কারেক্ট এগেন।” ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, “তুমি বলেছিলে, বিমলভূষণের বিষয়। আশয় নুটু যেভাবে সামলাচ্ছে, তাতে তাকে একজন ঝানু লোক বলেই তোমার মনে হয়। তোমার কথা শুনে আমার মনে প্রশ্ন জাগে যে, এত বড় সম্পত্তির দায়িত্ব যার হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে, তলে-তলে সে নিজের আখের গোছাচ্ছে না তো? কিংবা, জুয়া-টুয়া খেলতে গিয়ে কোনও বড় রকমের আর্থিক সমস্যায় পড়ে যায়নি তো? তা এক ঝানু লোকের সম্পর্কে জানতে হলে আর-এক ঝানু লোকের কাছে যাওয়াই ভো নিয়ম, তাই না?”
সদানন্দবাবু বললেন, “বুজিছি। সেই জন্যেই আপনি আদিনাথবাবুর কাঁচে গেসলেন।
ভাদুড়িমশাই বললেন, “ঠিক ধরেছেন। আসলে, হিরের দিকে কে কে হাত বাড়াতে পারে, সেটা ভাবতে গিয়ে নুটুকেও আমার লিষ্টি থেকে আমি বাদ দিইনি। তা আদিনাথ যা বলল, তাতে মনে হল, আমার সন্দেহটা মিথ্যে নয়।
“অর্থাৎ যে রক্ষক, সে-ই ভক্ষক! বিমলভূষণের সম্পত্তির একটা মস্ত অংশ টু হাতিয়ে নিয়েছে, কেমন?”
“না, সদানন্দবাবু,” ভাদুড়িমশাই বললেন, “এটা আপনি ঠিক কথা বললেন না। সম্পত্তি নই হাতায়নি। টাকাকড়িও না। শুধু তা-ই নয়, পুরনো সম্পত্তি তো সে আগলে রেখেছেই, তার উপরে নতুন সম্পত্তি যা কিছু কিনেছে, তা সবই কিনেছে বিমলভূষণের নামে। সেদিক থেকে সে মোলো-আনার উপরে আঠারো-আনা সৎ। অথচ এক্ষুনি যে তার লাখ-লাখ টাকা দরকার, তাও ঠিক।”
সদানন্দবাবুর মুখ দেখে মনে হল, তিনি ধাঁধায় পড়ে গেছেন। বললেন, “তা কী করে হয়?”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “কী করে হয়, তা আদিনাথের কাছেই জানা গেল। সে-ই বলল যে, বছর পাঁচেক আগে বিমলভূষণের নামে সে লাখ পঁচিশেক টাকার শেয়ার কিনেছিল, অ্যাট পার। শেয়ারগুলোর দাম আস্তে-আস্তে বাড়ছিলও। ইন ফ্যাক্ট যদি বছর দুয়েক আগেও বেচে দিত, তা হলে লাভ নেহাত খারাপ থাকত না। কিন্তু তখন বেচেনি। আর তারপরেই দাম হঠাৎ পড়তে শুরু করে।”
জিজ্ঞেস করলুম, “পড়তির মুখেও ছেড়ে দেয়নি?”
‘না। ভেবেছিল এটা সাময়িক ব্যাপার, দাম আবার উঠবে। কিন্তু ওঠা তো দূরের কথা, দাম আরও পড়ে যায়। দশ টাকার যে শেয়ার বাইশ টাকায় উঠেছিল, তা এখন পাঁচ থেকে ছ’টাকার মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে।”
“ওরে বাবা,” পরমেশ বললেন, “সে তো অনেক টাকার লোকসান।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “আদিনাথ বলল, দাম যেখানে উঠেছিল, সে-কথা ভুলে গিয়ে যদি পারচেজ-প্রাইসের কথাও ভাবা যায়, তো লোকসান তা ধরো দশ-বারো লাখ টাকার।”
একটুক্ষণের জন্যে চুপ করে রইলেন ভাদুড়িমশাই। তারপর বললেন, “তো আমার সন্দেহ হল, হিরে দুটো হাতিয়ে গোপনে বেচে দিয়ে সেই টাকায় নুটু ওই দশ-বারো লাখের ঘাটতি মেটাবার কথা ভাবছে না তো? আজ ভোরে হরপার্বতীর চোখে যখন হিরে পরানো হয়, গেস্ট হাউসের বারান্দা থেকে নুটুর উপরে তখন তাই কড়া নজর রেখেছিলুম। দেখছিলুম, হিরের দিকে সে হাত বাড়ায় কিনা।” ।
আমি বললুম, “সে-দুটো অবশ্য আসল হিরে নয়, নকল হিরে।”
“তা হোক,” ভাদুড়িমশাই বললেন, “নুটু তো সেকথা জানত না। হাত বাড়ালে সে আসল হিরে ভেবেই বাড়াত।”
সদানন্দবাবু বললেন, “অথচ অন্ধকারে নুটুর বদলে হাত বাড়াল তার ওয়াইফ! হরি হরি!”
ঠাট্টা করবেন না, ঠাট্টা করবেন না।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “সাধ্বী স্ত্রীর যা করা উচিত বলে নুটুর বউয়ের মনে হয়েছিল, সে তা-ই করেছে। নুটু নিজের আর্থিক সমস্যার কথা তাকে জানিয়েছিল কি না, তা আমি জানি না। হয়তো জানিয়েছিল, হয়তো জানায়নি। কিন্তু যদি নাও জানিয়ে থাকে, তবু সে আঁচ করেছিল নিশ্চয়। তা নইলে কেন বিগ্রহের চোখের দিকে সে হাত বাড়াবে? নুটুকে তার আর্থিক সমস্যা থেকে সে উদ্ধার করতে চেয়েছিল। তবে আমার বিশ্বস টু সেকথা জানত না।”
আমি বললুম, “তা তো হল, কিন্তু অত তাড়াতাড়ি ওই নকল চোখজোড়া আপনি জোগাড় করলেন কীভাবে? সাইজ আর শেপ তো বলতে গেলে একেবারে একইরকম। চট করে কোনও পার্থক্যও তো কেউ ধরতে পারবে না।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “তার কৃতিত্ব আমার দ্বিতীয় বন্ধুটির, অর্থাৎ শ্ৰীমন্ত বসাকের। সে যে এখানকার একজন নামজাদা জুয়েলার, তা তো পরমেশের মুখেই শুনলেন। এও শুনলেন যে, সে সোনার গয়না ছাড়া নানারকম প্ৰেশাস স্টোনেরও কারবারি। তা কাজ করা কাঁচের স্টকও তার কম নয়। আংটি কিংবা দুলে কিংবা নাকছাবিতে যারা নানা রঙের পাথর বসিয়ে নেয়, তাদের সবারই কি আর হিরে-চুনি-পান্না বসাবার মতো পয়সা আছে? পয়সা না থাকলে মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ, অর্থাৎ হিরে-চুনি-পান্নার বদলে তারা কাঁচ বসায়।”
একটুক্ষণের জন্যে চুপ করলেন ভাদুড়িমশাই। ফের একটা সিগারেট ধরালেন। তারপর তার আগের কথার জের টেনে বললেন, “তা কাল দুপুরে সেনেদের বাড়িতে গিয়ে হিরে দুটিকে যখন প্রথম দেখি, তখনই বেশ ভাল করে তার শেপ আর সাইজ আমি দেখে নিই। গেস্ট হাউস থেকে কাল দুপুরে ফের একবার বেরিয়েছিলুম, আপনাদের মনে পড়ে?”
বললুম, “হ্যাঁ, গৌরাঙ্গ ভট্টচাজের সঙ্গে কথা শেষ করার পরেই আপনি গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যান। তারপর পাঁচটা নাগাদ গেস্ট হাউসে ফিরে আসেন। কোথায় গিয়েছিলেন?”
“তাও বলতে হবে?” ভাদুড়িমশাই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “নাঃ কিরণবাবু, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না। সত্যিই আপনি দিনে দিনে একটি বাঁধাকপি হয়ে যাচ্ছেন!”
সদানন্দবাবু বললেন, “নিশ্চয় আপনার সেই জুয়েলার বন্ধুর বাড়িতে গেলেন?”
ভাদুড়িমশাই ফের আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “এই দেখুন, সদানন্দবাবু ঠিক ধরেছেন।…হ্যাঁ, শ্ৰীমন্তের কাছেই গেসলাম। তবে তার বাড়িতে নয়, দোকানে। সেনেদের হিরের সাইজ আর শেপ তো আমার স্মৃতিতে একেবারে গাঁথাই ছিল, তাই কাগজে সে দুটোকে এঁকে দেখাতে কোনও অসুবিধেই হল না। শ্ৰীমন্তও সঙ্গে-সঙ্গে নানান সাইজের নানান শেপের আর নানান নকশার কাজ করা এক বাক্স কাঁচ আমার সামনে এনে বলল, এর থেকে বেছে নাও।”
“বেছে নিলেন?”
“আমাকে আর কষ্ট করে বাছতে হল না। ওর দোকানেরই এক কর্মচারী এসে আমারই আঁকা ছবির সঙ্গে মিলিয়ে আমাকে বেছে দিলেন। দেখলুম, যা চেয়েছিলুম, একেবারে সেই জিনিসটিই পেয়েছি।
পরমেশ বললেন, “তারপর?”
ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, “তারপর আর কী, কাল রাত্তিরে তো সেনেদের বাড়িতে খেতে গেসলুম। তখন আসল হিরেজোড়া আমার হাতে চলে এল, আর নকল হিরে ঢুকে গেল ভেলভেটের বাক্সে। এটা কীভাবে হল, সেটা আজই এঁদের সামনে একবার বলেছি, তুমি এঁদের কাছ থেকে জেনে নিয়ো। কিন্তু আর নয়, যা গরম পড়েছে, এইভাবে আর বসে থাকা যাচ্ছে না। চলি হে পরমেশ, ঘরের জানলাগুলো বন্ধ করে, ফুল স্পিডে পাখা চালিয়ে একটু গড়িয়ে নেওয়া যাক্। আর হ্যাঁ, বুঝতেই তো পারছ, এর সঙ্গে একটা ফ্যামিলির মান-সম্মানের প্রশ্নও জড়িয়ে রয়েছে। তাই যা-যা শুনলে, তা যেন কক্ষনো কাউকে বোলো না।”
পরমেশ হেসে বললেন, “পাগল! তা কখনও বলা যায়?”
সোফা থেকে উঠে ভাদুড়িমশাই তার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন। যেতে-যেতেই ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, “চুরির ব্যাপারে না থাক, ও-বাড়ির চেহারায় কিন্তু ফ্রেঞ্চ কানেকশনটা রয়েই গেল। সেটা লক্ষ করেছেন সদানন্দবাবু?”
সদানন্দবাবু বললেন, “তা করিচি বই কী। দেওয়ালে টাঙানো অয়েল পেন্টিংয়ের কতা বলচেন তোতাতে কালীভূষণের চোক কালো হলে কী হয়, তার ছেলে কীর্তিভূষণের চোক নীল।”
“তারপর এক পুরুষ অর্থাৎ চন্দ্রভূষণকে বাদ দিয়ে আমাদের বিমলভূষণের চোখেও সেই নীল রং এসে ঢুকে পড়েছে।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “একে কী বলে জানেন তো? আটাভিজম।”
বলে আর অপেক্ষা করলেন না ভাদুড়িমশাই, দরজার পর্দা সরিয়ে তার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।
ঘণ্টা দুয়েক গড়িয়ে নিয়ে বিকেলে একবার সবাই মিলে ভদ্রেশ্বরে যাওয়া হয়েছিল। লুই আঁতোয়নের চিঠিখানা হরসুন্দরবাবুকে ফিরিয়ে দিয়ে এসেছি। ভদ্রলোককে বড়ই বিমর্য মনে হল। মানতের চুল আগেভাগেই কেটে দিয়েছেন বলে যেমন পাড়ার পাঁচজনের কাছে তেমন নিজের বাড়িতেই তাকে বোধহয় খুবই হোস্তা হতে হয়েছে।
ভদ্রেশ্বর থেকে একেবারে সরাসরি আমরা চন্দননগরের স্ট্র্যান্ডে চলে যাই। সেখানে গঙ্গার ধারে রাত প্রায় আটটা অব্দি বসে গল্পগুজব করি। একটু আগে পরমেশের বাড়িতে ফিরে স্নান করে রাতের খাওয়া সেরে নিয়েছি। এখন ছাতের উপরে মাদুর বিছিয়ে বসে চলছে আড্ডা।
তারই মধ্যে হঠাৎ ভাদুড়িমশাই বললেন, “একটা ব্যাপার কিন্তু বোঝা গেল না। আজ সকালে মন্দির-চত্বরে ওই যে মেন সুইচ অফ করে আলো নিবিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ওটা কে করল?”
সদানন্দবাবু বললেন, “তা জানি না, তবে আলো নিববার আগে কিন্তু একটা লোককে খুবই সন্দেহজনকভাবে আমি ওখানে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছিলুম। লোকটা যেমন বেঁটে, তেমনি কালো। তা ছাড়া তার গালে বেশ বড়সড় একটা আঁচিলও দেখেছি।”
আমি বললাম, “এ তো গৌরাঙ্গ ভটচাজের দেওয়া বর্ণনার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। গঙ্গার ঘাটে গৌরাঙ্গ অবশ্য দু’জন লোককে হিরে নিয়ে কথা বলতে শুনেছিল। অন্যজনও কালো, তবে বেঁটে নয়, ঢ্যাঙা।”
“ঢ্যাঙাটা হয়তো ভিড়ের মধ্যেই ছিল।” ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, “হয়তো দু’জনে মিলে প্ল্যান এঁটেছিল যে, বেঁটেটা মেন-সুইচ অফ করে দিলেই ঢ্যাঙাটা অমনি অন্ধকারের মধ্যে ছিনিয়ে নেবে হরপার্বতীর চোখ। ইতিমধ্যে আরেকজনও যে হিরে চুরির ধান্ধায় আছে, তা তারা জানত না।….তবে আমার কী মনে হয় জানেন? নুটুর বউ যে হিরে চুরির প্ল্যান এঁটেই মন্দিরে এসেছিল, তা নয়। হঠাৎ একটা সুযোগ এসে যাওয়ায় অন আ সাডেন ইমপালস সে ওটা করেছে। মানে অন্যেরা জমি তৈরি করে দিল, অ্যান্ড শি জাসট রিপড় দ্য হারভেস্ট!”
পরমেশ চৌধুরি বললেন, “একেই বলে চোরের উপর বাটপাড়ি?”
আমরা হেসে উঠলুম।
ভুতুড়ে ফুটবল
ভুতুড়ে ফুটবল – গোয়েন্দা ভাদুড়িমশাই – নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
“এ তো বড় অদ্ভুত ব্যাপার, মামাবাবু!” হাতের কাগজ থেকে মুখ না তুলেই কৌশিক বলল, “আমাদের জার্নালিস্টদের কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? এদের কি কাণ্ডজ্ঞান বলে। কিছু থাকতে নেই?”
কথাটা ভাদুড়িমশাইয়ের উদ্দেশে বলা হয়েছিল, কিন্তু তিনি কোনও উত্তর দিলেন না। সম্ভবত কিছু শুনতেই পাননি। না-পাওয়াই স্বাভাবিক। কেন না, নিবিষ্টচিত্তে তিনি এখন ইস্টার্ন কুরিয়ার’-এর আজকের ওয়ার্ড-জাম্বলের উত্তর খুঁজছেন।
নিজে যেহেত খবরের কাগজে কাজ করি, তাই কী খবর দেখে জার্নালিস্টদের কাণ্ডজ্ঞান সম্পর্কে কৌশিকের হঠাৎ সন্দেহ দেখা দিল, এই পালটা প্রশ্নটা করতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু মুখ খুলবার ফুরসত পেলুম না, সদানন্দবাবু একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন, “ঠিক বলেচ, লাক কতার এক কর্তা বলেচ! আরে ছ্যা ছ্যাঁ, এই কি তোদের কাণ্ডজ্ঞান? দেকতে পাস না চোকের সামনে কী হচ্চে?”
অরুণ সান্যাল একটা সদ্য-আসা মেডিক্যাল জার্নালের পাতা ওলটাচ্ছিলেন। সেটা সরিয়ে রেখে বললেন, “কী হচ্ছে বোসদা?”
“বাঃ, তাও বলে দিতে হবে?” সদানন্দবাবু তার গলার পর্দা আরও এক ধাপ চড়িয়ে বললেন, “শহরটা যে চোর ছ্যাচড়ে আর গুণ্ডা-বদমাসে ভরে গেল, মশাই! আজ এখোনে ফ্ল্যাটে ঢুকে বন্দুক উঁচিয়ে ডাকাতি করছে তো কাল ওভেনে দিন-দুপুরে বোম ফাটিয়ে টাকার থলে কেড়ে নিচ্ছে! আর খবরের কাগজের লোকগুলোও হয়েছে তেমনি। এই যে ল-লেসনেস, কোতায় এর এগেস্টে রোজ একটা করে কড়া এডিটোরিয়েল লিকবি, তা নয়, তোরা আছিস শুদু পলিটিকস নিয়ে! কে কাকে নিকম্মার ধাড়ি বলেচে আর কার বউ। সরকারি বাড়িতে খাটাল বসিয়ে লাখ টাকার দুধ বিক্রি করচে! তা বলুক না, করুক না! নিকম্মাই বলুক আর অকম্মাই বলুক, দুধই বেচুক আর রাবড়িই বেচুক, তাতে তোর কী! খালি পলিটিক্স আর পলিটিকস! ঠিক বলেচ কৌশিক বাবাজি, এই পলিটিক্সই আমাদের ডুবিয়ে ছাড়ল!”
কৌশিক বলল, “যাব্বাবা! আমি মোটেই পলিটিকসের কথা ভাবছি না।”
সদানন্দবাবু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললেন, “পলিটিক্স নয়? তা হলে?”
ভাদুড়িমশাইয়ের জাম্ব মিলে গিয়েছিল। মৃদু গলায় বললেন, “হয়েছে। একটা ‘ই’ পাচ্ছিলুম না। তা উলটে-পালটে ‘সেনল্যাক’ যদি ক্যানসেল হয় তো তার মধ্যেই তো ‘ই’ পেয়ে যাচ্ছি। সব মিলিয়ে ম্যাজিক ওয়র্ডটা তা হলে দাঁড়াল ‘ক্রিকেট’। ও হ্যাঁ, তুই যেন কী বলছিলি কৌশিক?”
“আমি পলিটিক্সের কথাও ভাবছিলুম না, ক্রিকেটের কথাও ভাবছিলুম না। যেখানে মাত্তর একশো কুড়িটা রান দরকার, সেখানে একশো রান তুলতেই যাদের কালঘাম ছুটে যায়, তাদের নিয়ে আবার ভাববার কী আছে?”
অরুণ সান্যাল বললেন, “তা হলে?”
“আমি ভাবছিলুম ফুটবলের কথা।”
“অ্যাঁ, ক্রিকেটের তুলনায় ফুটবলটা কি আমরা ভাল খেলছি নাকি?”
“চুনি-পি কেবলরামের সময়ে যা খেলতুম, সেই তুলনায় অর্ধেক ভালও খেলছি না; তবে হ্যাঁ, মাঝখানে যে অধঃপতনটা ঘটেছিল, সেটা একটু সামলে নেওয়া গেছে। এবারকার ন্যাশনাল লিগ আর নেহরু কাপের খেলা দেখে অন্তত সেইরকমই মনে হল।”
একটুক্ষণ চুপ করে রইল কৌশিক। তারপর বলল, “কিন্তু মুশকিলটা কী হয়েছে জানো বাবা?”
অরুণ সান্যাল ফুটবল বলে কথা নেই, কোনও খেলারই খবর বিশেষ রাখেন না। মাঠ-ময়দানের ব্যাপার-ট্যাপার নিয়ে আসলে কোনও উৎসাহই নেই তার। তবু ছেলের কথার উত্তরে কিছু একটা না বললে ভাল দেখায় না বলেই আমতা-আমতা করে বললেন, “কেন, আবার কী মুশকিল হল?”
“কী মুশকিল হল, সেটা কিরণমামাকে জিজ্ঞেস করো।” বলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “এই তোমরা মানে জার্নালিস্টরাই হচ্ছে যত নষ্টের গোড়া। ফুটবলে আমাদের পারফরম্যান্সের গ্রাফের লাইনটা যেই না একটু উপরে উঠতে শুরু করেছে, অমনি তোমরা এমন হই-হই বাধিয়ে দিলে যে, আর দেখতে হবে না, লাইনটা আবার মুখ থুবড়ে পড়ল বলে!”
কথার ঝাঁঝ থেকেই বোঝা যাচ্ছিল কৌশিক বেশ রেগে গেছে। কিন্তু রাগের কারণটা যে কী, সেটাই ঠিক ধরতে পারছিলুম না। ভাদুড়িমশাই, সদানন্দবাবু আর অরুণ সান্যালের মুখ দেখে মনে হল, তারাও কিছুই ধরতে পারেননি। ভাদুড়িমশাই বললেন, “একটু বুঝিয়ে বলবি?”
সদানন্দবাবু বললেন, “হ্যাঁ হ্যাঁ, একটু বুজিয়ে বলো তো।”
“এর মধ্যে আর বোঝাবুঝির কী আছে?” কৌশিক তার হাতের ‘বিশ্ববার্তা’ কাগজখানা আমার দিকে এগিয়ে ধরে, খেলার পাতার একটা তিন-কলম-জোড়া হেডলাইনের উপরে আঙুল রেখে বলল, “পড়ে দ্যাখো, তা হলেই সব বুঝতে পারবে।”
বিশাল টাইপের বিরাট হেডলাইন, ‘যে গোল দেখলে পেলে আর মারাদোনাও তাজ্জব হয়ে যেত!
সদানন্দবাবু বললেন, “পড়ে শোনান, পড়ে শোনান, আমরাও শুনতে চাই।”
অগত্যা যেমন হেডলাইন তেমন কোচি থেকে পাঠানো প্রতিবেদনও পড়ে শোনাতে হল। বিশ্ববার্তার স্পোর্টস রিপোর্টার ধনঞ্জয় চাকলাদার লিখছেন : “উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে আমাদের আই, এম, বিজয়ন যে গোলটি করলেন, তাকে বিশ্বমানের গোল বললেও খুব কমই বলা হয়, কেন না ইউরো কাপ আর কোপা আমেরিকার কোনও খেলাতেই এমন অত্যাশ্চর্য গোল দেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। এমন কী, গত তিন বারের বিশ্বকাপেও না। দুদিকে দুই হুমদো-জোয়ান উজবেক ডিফেন্ডার, ভাল করে ঘুরে দাঁড়াবার জায়গাটুকু না রেখে তারা বিজয়নের গায়ের সঙ্গে একেবারে আঠার মতন সেঁটে রয়েছে, অথচ তারই মধ্যে সামান্য একটু টলে গিয়ে, বলটাকে অল্প তুলে নিয়ে, মুখ না ঘুরিয়েই বিজয়ন যে বাইসিকল কিক করলেন, গোলকিপারের মাথার উপর দিয়ে তাতেই বল গিয়ে জালে জড়িয়ে গেল। এ একেবারে অর্জুনের লক্ষ্যভেদ। দর্শকরা প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেননি, তারপরেই তারা উল্লাসে ফেটে পড়েন। উন্নাস স্বাভাবিক, কেন না অনেক ভাগ্য করে জন্মালে তবেই এমন একটি গোল দেখার সুযোগ পাওয়া যায়। সত্যি বলতে কী, পেলে আর মারাদোনাও এই গোল দেখলে তাজ্জব হয়ে যেতেন। তবে আমার ধারণা, ভারতের মাঠে এই ধরনের গোল হয়তো আমরা আর দেখতে পাব না, কেন না বিদেশিরাও বিজয়নের এই খেলা টিভির পর্দায় দেখেছে নিশ্চয়, এবং এই গোলের পরে ব্রিটেনের ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড, স্পেনের রিয়েল মাদ্রিদ, হল্যান্ডের আয়াক্স, ইতালির এ সি মিলান ও আর্জেন্টিনার বোকা জুনিয়র্স থেকে বিজয়নের ডাক পড়তে বাধ্য। আসন্ন, অনিবার্য সেই দিনটিকে আজ আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, এইসব বিশ্ববিখ্যাত ক্লাবের ধনকুবের কর্তারা যখন চেকবই হাতে নিয়ে বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনের জাম্বো জেট থেকে দিল্লি, কলকাতা, মুম্বই কি চেন্নাই এয়ারপোর্টে এসে নামবেন ও নেমেই কানেকটিং ফ্লাইট ধরে যাত্রা করবেন তিরুবনন্তপুরমের দিকে, এবং…”
.
“থাক্, থাক্, কিরণমামা, আর পড়ার দরকার নেই।” পুরো সেনটেন্সটা কমপ্লিট করার আগেই কৌশিক আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, “যেটুকু পড়েছ, তাতেই তোমাদের জার্নালিস্টদের কাণ্ডজ্ঞানের বহরটা টের পাওয়া যাচ্ছে, এর পরে তুমি নিজেই বোধহয় বিষম খেতে শুরু করবে!”
কাগজ থেকে মুখ তুলে দেখলুম, ভাদুড়িমশাই আর অরুণ সান্যাল মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাসির বেগ সামলাচ্ছেন। তারই মধ্যে সদানন্দবাবুকে দেখে একটু অবাক হতে হল। কেন না, একমাত্র তারই মুখে হাসি নেই। গম্ভীর গলায় বললেন, “এতে এত হাসির কী আচে?”
কৌশিক বলল, “নেই? তার মানে আপনিও মনে করেন যে, ভাল একটা গোল করেছে বলেই বিশ্ববিখ্যাত এইসব ক্লাব অমনি বিজয়নকে নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করে দেবে?”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “ডেসক্রিপশান থেকে তো মনে হচ্ছে…মানে অন্য সব কাগজও দেখলুম তো…তাতে তো বলতেই হয় যে, গোলটা সত্যিই চমৎকার দিয়েছে।”
“আহা-হা, আমি কি বলছি যে, ওটা চমৎকার গোল নয়? অফ্ কোর্স ইট ওয়াজ আ ব্রিলিয়ান্ট গোল! কিন্তু তাই বলে যদি কেউ বলে যে, পেলে আর মারাদোনাও এই গোলটা দেখলে তাজ্জব হয়ে যেত, তো আমি বলব তার কাণ্ডজ্ঞান বলতে কিসসু নেই!”
“দ্যাকো কৌশিক, সদানন্দবাবু বললেন, “এর মদ্যে তুমি দু-দুবার পেলে আর মারাদোনার নাম করেছ। তো একটা কতা তোমাকে জিগেস করতে পারি?”
“করুন।”
“এঁয়ারা কারা?”
“যাব্বাবা,” হতভম্ব হয়ে কৌশিক বলল, “এরা কারা, আপনি জানেন না? এঁরা হচ্ছেন সেই তারা, ফুটবলে যাদের অল-টাইম গ্রেট বলা হয়। কেন, টিভিতে আপনি মারাদোনার খেলা দেখেননি?”
সানন্দবাবুর মুখ দেখে মনে হল না যে, কৌশিকের কথা শুনে তিনি বিন্দুমাত্র দমে গিয়েছেন। একই রকমের গম্ভীর গলায় বললেন, “না হে, দেকিনি। কিন্তু তাতে হলটা কী?”
কৌশিক হেসে বলল, “কী আর হবে, একজন জিনিয়াস কীভাবে ফুটবলটাকে নিয়ে যা-খুশি তা-ই করতে পারে, সেটা দেখতে পাননি, এই আর কী।”
“বটে? তা ফুটবল নিয়ে যা-খুশি তা-ই কি একা ওই লোকটাই করতে পারত?”
“আর-কেউ পারত…মানে পেলের পরে এক ওই মারাদোনা ছাড়া আর কেউ পারত বলে তো জানি না।” ঠাট্টার গলায় কৌশিক বলল, “কেন, আপনি কি জানেন নাকি?”
সদানন্দবাবু তক্ষুনি এই প্রশ্নের জবাব দিলেন না। চা এসে গিয়েছিল। নিজের পেয়ালায় আলতো একটা চুমুক দিয়ে পেয়ালাটাকে ধীরেসুস্থে পিরিচের উপর নামিয়ে রেখে তিনি কৌশিকের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, “হাবল। বাঁড়ুজ্যের খেলা দেকেচ?”
এবারে কৌশিকেরই ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়ার পালা। আমতা-আমতা করে বলল, “না
“কী করেই বা দেকবে।” ঠোঁট বেঁকিয়ে সদানন্দবাবু বললেন, “তোমার তো কতাই ওটে না, তোমার বাবাও তখনও জন্মাননি।”
অরুণ সান্যাল বললেন, “অ্যাঁ, বলেন কী! তিনি কবেকার মানুষ?”
“ফাস্ট ওয়ার্লড ওয়ার তো ১৯১৪ সালে লাগে, তিনি তারও বারো বছর আগে, অর্থাৎ নাইনটিন হানড্রেড টু’তে জন্মেছিলেন। ছেলেবেলায় আমরা তার খেলা দেকিচি। উঃ, সে কী খেলা রে বাবা, হরিচরণ মেমোরিয়াল শিল্ডের খেলায় উঁচড়ো ইউনাইটেডকে একাই এক ডজন গোল দিয়েছিলেন।”
কৌশিক বলল, “কলকাতায় খেলতেন?”
“আমাদের ময়দানের কতা বলছ তো? মাত্তর একবারই এখেনে খেলতে নেবেছিলেন। এ হল নাইনটিন টুয়েন্টির কতা। গোরা টিমের সঙ্গে ফ্রেন্ডলি ম্যাচ। সায়েবগুলোকে তাতেই এমন কঁদিয়ে ছাড়েন যে, সেই রাত্তিরেই গলির ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তারা একজন মেসেঞ্জার পাটিয়ে দেয়। মেসেঞ্জার গিয়ে হাকিমকে বলে, স্টপ দিস হালা বাঁড়ুজ্যে, ডিফেন্স অব ইন্ডিয়া আইনে ওর মুভমেন্ট রেসট্রিকট করো, ওকে যদি কলকাতায় আসতে দাও, তা হলে এখেনে ল অ্যান্ড অর্ডার মেনটেন করা যাবে না, ব্রিটিশ গবরমেন্টের প্রেস্টিজ ও একেবারে পাংচার করে দেবে। ব্যস, হালা বাঁড়ুজ্যে তার পরদিন তারকেশ্বর লাইনের নসিপুরে তার বাড়িতে ফিরতেই কুম জারি হয়ে গেল যে, হুগলি জেলার চৌহদ্দি ছেড়ে তিনি কোতাও যেতে পারবেন না। তার ফল কী হল, ভাবতে পারো?”
“কী হল?”
“নাইনটিন টুয়েন্টিতেই মোহনবাগান ফর দি সেকেন্ড টাইম আই এফ এ শিল্ড জেতার যে চেষ্টা চালাচ্ছিল, আর তার জন্যে হাবলা বাঁড়ুজ্যেকে টিমে ঢোকাবার ব্যবস্থা একেবারে পাকা করে ফেলেছিল, সেটা আর সাকসেসফুল হল না।”
“এ সব কথা আপনি কার কাছে শুনলেন?”
“কেন, আমার বাবার কাছে।” চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে সদানন্দবাবু বললেন, “ওহে বাপধন, সারা জীবন সায়েব চরিয়ে খেয়েচি, সায়েব চিনতে আর আমার বাকি নেই। ওদের মদ্যে আমাদের কোম্পানির জেঙ্কি সায়েবের মতো ভাল মানুষ যেমন আচে, তেমনি কুচুটে বজ্জাতও কি কিছু কম আচে নাকি? তা যদি না থাকত, তো মারাদোনার নাম না কপচে তোমরা আজ হাবলা বাঁড়ুজ্যেকে মাথায় তুলে নাচতে।”
ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, তার চোখের মধ্যে ঈষৎ কৌতুকের ছোঁয়া লেগেছে, তবে হাসিটাকে তিনি ঠোঁট পর্যন্ত আসতে দিচ্ছেন না। বললেন, “একটু আগে বলছিলেন যে, ছেলেবেলায় আপনি তার খেলা দেখেছেন। এটা কোথায় দেখলেন?”
“সিঙুরে।” সদানন্দবাবু বললেন, “তারকেশ্বর বলতে যে জায়গাটা আপনারা বোজেন, আমরা তো ঠিক সেখেনকার লোক নই। ওর খুব কাঁচেই হচ্ছে সিঙুর। আমরা সেই সিঙুরের বাসিন্দা। সেখানকার মাঠে হাবলা বাঁড়ুজ্যের খেলা আমি ফর দি ফাস্ট টাইম দেকি। আমার বয়স তখন আব কত হবে, মেরেকেটে পাঁচ কি ছয়। সেদিনকার খেলার ডিটেলস আমার মনে নেই, তবে এটা ভুলিনি যে, হাফটাইমের আগেই একটা লোক দমাদ্দম চার-পাঁচটা গোল হাঁকড়ে দিয়েছিল। পরে শুনলুম, সে-ই হচ্চে হাবলা বাঁড়ুজ্যে।”
“দ্বিতীয়বার তাঁর খেলা কবে দেখলেন?”
“ইন দি ইয়ার নাইনটিন ফফটি টু।” সদানন্দবাবু বললেন, “জাপানিরা হাতিবাগানে বোমা ফেলেছিল বলে আমরা সেবার কলকাতার পাট তুলে দিয়ে মাস ছয়েকের জন্যে আমাদের গ্রামের বাড়িতে চলে যাই।”
“নাইনটিন ফর্টি টু?“ ভাদুড়িমশাই বললেন, “আপনারই হিসেবে হাবলা বাঁড়ুজ্যের বয়েস তো তখন চল্লিশ হয়ে গেছে!”
“তা তো হয়েইছে। কিন্তু এই বুড়ো হাড়েই যা ভেলকি দেকালেন না…উফ!” সদানন্দবাবু দু’ হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বললেন, “অপূর্ব, অপূর্ব! সেই খেলাতেই তো চুচড়ো ইউনাইটেডকে গুনে-গুনে এক ডজন গোল দেন! কী বলব মশাই, খেলাটা যেন এখনও আমার চোকের সামনে ভাসচে! ইদিকে হাল্লা, ওদিকে হালা, সিদিকে হাল্লা…যেদিকে তাকাই, শুধু হাল্লা আর হাল্লা! গোটা মাঠে তাকে ছাড়া কাউকে দেতে পাই না! ভাবা যায়?”
একটুক্ষণের জন্য চুপ করলেন সদানন্দবাবু। তারপর একটু গলা নামিয়ে বললেন, “কিন্তু তার এক হপ্তা বাদেই ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা! উঃ, সেকতা ভাবলে এখনও গায়ে কঁটা দেয়।”
কৌশিক কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু সদানন্দবাবুর শেষ কথাটায় একটা রোমাঞ্চকর গল্পের গন্ধ পেয়ে যাওয়ায় অরুণ সান্যাল তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, “আঃ, তুই দেখছি বকরবকর করেই সক্কলের মাথা ধরিয়ে দিবি। একটু চুপ কর তো। …নিন বোদা, কী ঘটেছিল বলুন।”
আজ রবিবার, ৬ এপ্রিল। কৌশিককে সঙ্গে নিয়ে ভাদুড়িমশাই গত শুক্রবার কলকাতায় এসেছেন। কৌশিক বুধবার বাঙ্গালোরে ফিরে যাবে, কিন্তু ভাদুড়িমশাই তাঁর সি বি আই অর্থাৎ চারু ভাদুড়ি ইনভেস্টিগেশনসের একটা আপিস যেহেতু এখানেও খুলতে চান, তাই পুরো মাসটাই তার কলকাতায় কাটাবার সম্ভবনা। কথা শুরু হয়েছিল এই আপিস ভোলার ব্যাপার নিয়েই। শুনলুম ক্যামাক স্ট্রিটে একটা আপিস বাড়ির দোতলায় বেশ খানিকটা ফ্লোর স্পেস পেয়েও গেছেন। তাতে পাটিশানের ব্যবস্থা করে দিব্যি তিনটে ঘর আর একটা অ্যাটাচড বাথ করে নেওয়া যাবে। চেনা একজন কন্ট্রাকটরের সঙ্গে তা-ই নিয়ে কথাও হয়ে গেছে তার। এখন একজন রিসেপশনিস্ট কাম টাইপিস্ট আর মোটামুটি কাজ জানা দু’জন লোক পেয়ে গেলেই হয়।
গত বছর এই সময়ে ভাদুড়িমশাইয়ের সঙ্গে দিন কয়েকের জন্যে একটা তদন্তের কাজে ইউ পি-র মির্জাপুরে যেতে হয়েছিল। তার পরে আর কোথাও যাওয়া হয়নি। শিগগির যে যাওয়া হবে, এমনও মনে হয় না। একে ভাদুড়িমশাইয়ের শরীর ইদানীং বিশেষ ভাল যাচ্ছে না, তার উপরে আবার এই নতুন আপিস নিয়ে বেশ কিছুদিন তাঁকে এখন ব্যস্ত থাকতে হবে। তাতে অবশ্য আমাদের বেজার হবার কিছু নেই। বরং আপাতত যে তিনি এখান থেকে নোঙর তুলবেন না, তাতেই আমরা খুশি।
কথাবার্তা দিব্যি এগোচ্ছিল। ইতিমধ্যে একগাদা খবরের কাগজ এসে যাওয়ায় সবাই তার উপরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ভাদুড়িমশাই ইস্টার্ন কুরিয়ারের ফাস্ট পেজের হেডলাইনগুলো দেখে নিয়ে ভিতরের পাতা খুলে জাম্বলের সমাধান করতে লেগে যান। সেন্টারে যুক্তফ্রন্ট থেকে কংগ্রেসের সমর্থন প্রত্যাহারের ফলে দেশের রাজনীতি এবার কোন দিকে মোড় নেবে, তা-ই নিয়ে অরুণ সান্যাল, কৌশিক, সদানন্দবাবু ও আমার মধ্যে আলোচনা চলতে থাকে। অরুণ সান্যাল তাতে বিশেষ উৎসাহ না পেয়ে খানিক বাদে একটা মেডিক্যাল জার্নাল টেনে নেন। কৌশিক ‘ধুর, রাজনীতি আবার ভদ্দরলোক করে!’ বলে খেলার পাতায় চলে যায়। আর তার পরে-পরেই তোলে সাংবাদিকদের কাণ্ডজ্ঞান নিয়ে সেই প্রশ্ন, যার উল্লেখ এই লেখার একেবারে গোড়াতেই করেছি।
অরুণ সান্যাল বললেন, “কী বোদা, চুপ করে আছেন কেন, গায়ে কাঁটা দেওয়ার মতো কী হয়েছিল, বলুন, এইভাবে দগ্ধে মারবেন না তো।”
মালতী রান্নার কাজে ব্যস্ত। তাই পার্বতী, মানে কাজের মেয়েটিকে দিয়ে ইতিমধ্যে সে এক প্লেট পকোড়া পাঠিয়ে দিয়েছিল। সদানন্দবাবু প্লেট থেকে আলগোছে একটি পকোড়া তুলে নিয়ে মুখের মধ্যে চালান করে বললেন, “ওরে ভাই, সে এক ভয়ংকর ব্যাপার! ওই যে খেলার কথা বললুম না, তার এক হপ্তা বাদেই কামারকুণ্ডুর যজ্ঞেশ্বর শিল্ডের সেমিফাইনালে আমাদের সিঙুরের টিম নাবাতে হবে এগেস্ট গুপ্তিপাড়া বুলেটুস। তো হাবলার সেদিনকার খেলা দেখেই আমাদের সিঙুর অ্যাথলেটিক ক্লাবের সেক্রেটারি রতনমণি সাঁতরা বললেন, ‘কোনো কতা নয়, এই নাও পঞ্চাশটা টাকা, এ আমি নিজের গাঁট থেকে দিচ্চি, এই টাকা নিয়ে কাল সকালেই নসিপুরে গিয়ে হালা বাঁড়ুজ্যেকে হায়ার করে ফ্যালো, নয়তো গুপ্তিপাড়ার যা মারকাটারি টিম, সেমিফাইনালে তারা আমাদের কাদিয়ে ছাড়বে। তো তা-ই হল।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “তা-ই হল মানে গুপ্তিপাড়া আপনাদের কাঁদিয়ে ছাড়ল?”
“আরে না মশাই, তা-ই হল মানে হাবলাকে আমরা হায়ার করে ফেললুম। আর সেমিফাইনালের খেলায় কোতায় গুপ্তিপাড়া আমাদের কাঁদিয়ে ছাড়বে, তা নয়, হাফ-টাইমের আগেই সাত-সাতটা গোল খেয়ে তারাই হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল। তাদের ক্যাপ্টেন এসে বলল, “মশাই, ম্যাচটা আমরা সারেন্ডার করে দিচ্চি। হালার সেভেন্থ গোলটা আটকাতে গিয়ে আমাদের গোলকিপারের পাজরার একখানা হাড় বোধহয় ভেঙে গেচে, রাইট আউট ন্যাংচাচ্চে, লেফট ব্যাকেরও কিছু একটা হয়েছে নিশ্চই, নয়তো ও ওরকম নেতিয়ে পড়ে কাতরাত না! এবারে আমাদের ভালয়-ভালয় বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করে দিন। বাস, ড্যাংডেঙিয়ে আমরা ফাইনালে উঠে গেলুম।”
অরুণ সান্যাল বললেন, “তারপর ফাইনালে ক’ গোলে জিতলেন?”
সদানন্দবাবু নিমপাতা-চিবোনো মুখ করে বললেন, “জিতলুম কোতায়, হেরে ভূত হয়ে গেলুম বাঁশবেড়ের হংসেশ্বরী স্পোর্টিং ক্লাবের কাছে। সেমিফাইনালে সাত গোলে জিতেছিলুম, তাও আদ্ধেক খেলা বাকি থাকতেই, আর ফাইনালে খেয়ে গেলুম আট গোল। কামারকুণ্ডুর স্পেক্টেটররা একেবারে ছ্যা ছ্যা করতে লাগল।”
“তার মানে হাবলা বাঁড়ুজ্যেকে আপনারা ফাইনাল খেলার দিন মাঠে নামাতে পারেননি?”
‘না মশাই, পারিনি।” সদানন্দবাবু বললেন, “অবিশ্যি সেমিফাইনালের দিনও যে তিনিই মাঠে নেমেছিলেন, তাও বলতে পারছি না।”
“তার মানে?”
প্লেট থেকে আর-একটা পকোড়া তুলে মুখের মধ্যে ফেলে দিয়ে সদানন্দবাবু বললেন, “বেড়ে করেছে কিন্তু। সকালে আমার সেকেন্ড কাপ খাওয়া হয়ে গেছে ঠিকই, তবে কিনা এর সঙ্গে আর-এক কাপ চা হলে মন্দ হত না।”
ভাদুড়িমাশাই হেসে বললেন, “এসে যাবে, এসে যাবে। তার আগে গপ্পোটা শেষ করুন তো। সেমিফাইনালের দিন কে তা হলে মাঠে নেমেছিল?”
“তা যদি বলতে পারতুম, তবে তো ল্যাটা চুকেই যেত। কিন্তু বলতে পারছি কোতায়?”
অরুণ সান্যাল সেই একই কথার পুনরুক্তি করলেন, “তার মানে?”
কাজের মেয়েটি দ্বিতীয় রাউন্ডের চা দিয়ে গেল। ট্রে থেকে লিকারের কাপটা তুলে নিয়ে তাতে আলতো করে ঠোঁট ঠেকিয়ে সদানন্দবাবু বললেন, “বলচি, বলছি। সেমিফাইনালেই হাবলার দাপট দেখে আমাদের সাঁতরা মশাই তক্ষুনি-তক্ষুনি ঠিক করে ফেলেছিলেন যে, ফাইনালের খেলাতেও একে চাই। খেলা শেষ হয়ে যেতেই তাই গাঁট থেকে আরও পঞ্চাশ টাকা বার করে হাবলার দিকে এগিয়ে ধরে তিনি বললেন, ‘ফাইনালের জন্যে এই টাকাটা দিয়ে তোমাকে বুক করে রাকলুম। জেতাতে পারো তো
আরও পাঁচশ টাকা দোব। কিন্তু তাতে কী হল জানেন?”
“কী হল?”
“হাবলা বাঁড়ুজ্যে বলল, নিজের হাতে তো আমি টাকা নিই না। কাল সকালে বরং এই টাকাটা আপনারা আমার মায়ের হাতে দিয়ে আসবেন। বাস, তারপর আর একটাও কতা না বলে হাবলা তার সাইকেলে উঠে চলে গেল।”
“পরদিন সকালে আপনারা তা হলে ফের নসিপুরে গেলেন?”
“তা গেসলম বই কী। গিয়ে দেকি হালার মা শুকনো মুকে বারান্দায় বসে আছেন। আমরা তাকে কিছু বলারও সুযোগ পেলুম না। তার আগেই তিনি তার আঁচলের গিট খুলে দশ টাকার পাঁচখানা নোট বার করে বললেন, ‘কিছু মনে কোরো না বাবারা, পরশু রাত্তির থেকেই আমার ছেলের ধুম জ্বর, তাই তোমাদের হয়ে কাল খেলতে যেতে পারেনি। যে টাকাটা দিয়ে গেলে, সেটা ফিরিয়ে নে যাও, বাবা। শুনে তো আমাদের চক্ষু চড়কগাছ! হাবলা বাঁড়ুজ্যে কাল তা হলে সেমিফাইনালের খেলায় নামেনি? একেবারে তার মতন দেকতে যে-লোকটা কাল সাত-সাতটা গোল দিল, তাও হাফটাইমের আগেই, সে তা হলে কে?”
কৌশিক তার বাপের বকুনি খেয়ে চুপ করে ছিল। কিন্তু কতক্ষণ আর মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকবে। বলল, “যাচ্চলে, হচ্ছিল ফুটবলের গল্প, তো দুম করে সেটাকে আপনি ভূতের লাইনে ঠেলে দিলেন! এটা কী রকমের ব্যাপার হল বোস-জেই?”
সদানন্দবাবু বললেন, “এতে এত আশ্চজ্জি হবার কী আছে? ভূতেদের কি ফুটবল খেলার শখ হয় না? নরমুণ্ড দিয়ে গেণ্ডুয়া খেলার ব্যাপারটা তা হলে এল কোথথেকে? ওহে বাপধন, আমাদের ময়দানে যারা বল পেটায়, তাদের সবাই যে তোমার-আমার মতন জেনুইন মানুষ, তা কিন্তু ভেবো না। অচেন, ওই ভিড়ের মধ্যে তেনারাও দু’চারজন আচেন।”
কথাটা আর এগোল না, কেন না এই সময়েই কলিং বেল বেজে উঠল। তার মিনিট খানেক বাদেই কাজের মেয়েটি এসে জানাল, এক ভদ্রলোক দেখা করতে চান। “বললেন যে, শক্তিগড় থেকে এয়েচেন।”
নাম বললেন না?” প্রশ্নটা অরুণ সান্যালের।
“বললেন তো। তবে সে আমি বলতে পারবনি।”
.
॥ ২॥
পার্বতী, মানে এ-বাড়ির কাজের মেয়েটি বলেছিল, ভদ্রলোক। ফলে আমি ধরে নিয়েছিলুম যে, দর্শনপ্রার্থী ব্যক্তিটি নিশ্চয় একজন বয়স্ক মানুষ হবেন। কিন্তু অরুণ সান্যাল তাকে ভিতরে পাঠিয়ে দিতে বলার একটু বাদে ডান হাতে একটা বড় সাইজের মাটির হাঁড়ি ঝুলিয়ে যে-ছেলেটি এসে ড্রয়িংরুমে ঢুকল, তার বয়স বোধহয় বছর কুড়ির বেশি হবে না। পরনে চকোলেট রঙের ট্রাউজার্স আর সাদা হাফহাতা শার্ট, পায়ে কাবুলি চপ্পল, হাইট প্রায় ছ’ ফুট, চোখ দুটি ঝকঝকে, চাউনি দেখে বেশ বুদ্ধিমান বলে মনে হয়। হাতের হড়িটি আলগোছে মেঝের উপরে নামিয়ে রেখে, শার্টের বুকপকেট থেকে একটা খাম বার করে আমাদের উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে ছেলেটি জিজ্ঞেস করল, “আপনাদের মধ্যে মিঃ ভাদুড়ি কার নাম?”
কোনও ব্যাপারে সন্দেহ বা ভয়ের কারণ ঘটলে সদানন্দবাবু সাধারণত যা করে থাকেন, এক্ষেত্রেও একটু আগে ঠিক তা-ই করেছিলেন। সম্ভবত তার ধারণা হয়েছিল যে, হাঁড়ির মধ্যে সাপ কিংবা কাকড়া বিছে থাকা কিছু বিচিত্র নয়। ফলে, মেঝের উপরে ছেলেটি হাঁড়ি নামিয়ে রাখার সঙ্গে-সঙ্গেই সদানন্দবাবু মেঝে থেকে সড়াক করে তার পা দু’টি সোফার উপরে টেনে নিয়ে একেবারে জোড়াসন হয়ে বসে পড়েছিলেন। সেই অবস্থায় আঙুল তুলে ভাদুড়িমশাইকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, “উনি।”
হাতের খামখানা ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে ছেলেটি বলল, “আমার নাম ভূতনাথ দত্ত। শক্তিগড়ের ডাক্তার কৃপানাথ দত্ত আমার জ্যাঠামশাই। তিনি এই চিঠিখানা আপনাকে পাঠিয়েছেন।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “বোসো।” তারপর খাম থেকে চিঠি বাব করে চটপট তার উপরে চোখ বুলিয়ে নিয়ে চিঠিখানাকে সেন্টার টেবিলের উপরে রেখে তার উপরে একটা পেপারওয়েট চাপা দিয়ে মৃদু হেসে বললেন, “কৃপানাথ কেমন আছে?”
“এখন ভালই আছেন।’ ছেলেটি বলল, “মাঝখানে জন্ডিস হয়ে মাস দুয়েক খুব ভুগলেন। ভীষণ দুর্বল হয়ে গেলেন। তারপর একটু থেমে থেকে বলল, “বললুম বটে এখন ভাল আছে, তবে দুর্বলতা এখনও পুরোপুরি কাটেনি। নয়তো তিনি নিজেই আসতে।…আপনি যাবেন তো? আমরা কিন্তু সবাই খুব আশা করে আছি।”
যাবার প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গিয়ে ভাদুড়িমশাই বললেন, “কৃপানাথ তো তোমার জ্যাঠামশাই। তা তুমি ওর কোন ভাইয়ের ছেলে?”
“ছোট ভাইয়ের।”
“তার মানে বিশ্বনাথের। বিশ্বনাথ যে ফুটবলটা দারুণ খেলত, তা নিশ্চয় জানো?”
“জ্যাঠামশাইদের কাছে শুনেছি। বড় জ্যাঠামশাই আর মেজো জ্যাঠামশাই দু’জনেই বলেন যে, বাবার মতন স্ট্রাইকার নাকি ও তল্লাটে খুব বেশি ছিল না।”
“শুধু ও তল্লাটে কেন, কোনও তল্লাটেই খুব বেশি ছিল না।” ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, “তোমার ঠাকুর্দা তো বিশ্বনাথকে কলকাতায় আসতে দিলেন না। তা যদি দিতেন তো এখানকার বড়-বড় ক্লাবগুলোতে ওকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত।”
ভূতনাথ বলল, “তার খেলা আপনি দেখেছেন?”
“দেখেছি বই কী।” একটু যেন আনমনা হয়ে গেলেন ভাদুড়িমশাই। তারপর একটা নিশ্বাস ফেলে মৃদু হেসে বললেন, “তোমার বয়েস এখন কত ভূতনাথবাবু?”
লজ্জিত গলায় ভূতনাথ বলল, “আমাকে বাবু’ বলবেন না, বাড়িতে সবাই আমাকে ভুতে বলে। আপনারাও তা-ই বলবেন।”
“ঠিক আছে, তা-ই বলব, তবে ‘বাবু’টাও ছাড়ব না। ধরে নাও যে, বাবুটা আমি আদর করে বলছি। তা ভুতোবাবু, তোমার বয়েস কত তা তো বললে না।”
“আজ্ঞে উনিশ চলছে। বর্ধমানে রাজ কলেজে পড়ি, এবারে বি, এ, ফাস্ট পার্টের পরীক্ষা দেব।”
“বাঃ, তা এখন তোমার যা বয়েস, তোমার বাবাকেও ঠিক সেই বয়েসেই আমি প্রথম দেখেছিলুম। সেও তখন ওই রাজ কলেজেই পড়ত। যেমন ছিল লেখাপড়ায় ভাল, তেমন খেলাধুলোয়। বল ট্র্যাপিং, ড্রিবলিং, শুটিং, কোনও ব্যাপারেই খামতি ছিল না। বডি সোয়ার্ভ করে, বিপক্ষের ডিফেন্ডারদের ঝটকা দিয়ে যেভাবে বেরিয়ে যেত, সে তো আমার চোখে আজও ভাসছে। তা ভুতোবাবু, ফুটবলটা তুমিও খেলল তো?”
“আজ্ঞে হ্যাঁ, খেলি।” সেই একই রকমের লজ্জিত ভঙ্গিতে ভূতনাথ বলল, “তবে বাবার কথা যা শুনি, তত ভাল খেলতে পারি না।”
মেঝেতে যে হাঁড়িটা নামিয়ে রাখা হয়েছে, সে সম্পর্কে সদানন্দবাবুর সন্দেহ ইতিমধ্যে কেটে গিয়ে থাকবে, নয়তো সোফা থেকে তিনি ফের মেঝেতে পা নামাতেন না। তবে সন্দেহের জায়গায় এখন যে কৌতূহল দেখা দিয়েছে, সেটা আর তিনি চেপে রাখতে পারছে না। কিছুক্ষণ ধরেই উশখুশ করছিলেন, এবারে গলা খাঁকরে বললেন, “একটা কথা জিজ্ঞেস করব?”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “কী জিজ্ঞেস করবেন, সে তো বুঝতেই পারছি। হাঁড়ির খবর জানতে চান, এই তো? তা শক্তিগড় থেকে যে হাঁড়ি এসেছে, তার মধ্যে কী থাকতে পারে বলে আপনার ধারণা?”
ভূতনাথের মুখ থেকে লজ্জার ভাবটা কেটে গিয়েছিল। হেসে বলল, “শক্তিগড়ের হেম ঘোষের দোকানের ল্যাংচা। বড় জ্যাঠামশাই আপনাদের জন্যে পাঠিয়েছেন।”
“তা তো হল,” ভাদুড়িমশাই বললেন, “কিন্তু যেতে পারব কি না, হুট করে এখুনি তা তো বলা সম্ভব নয়। তুমি কি আজকের দিনটা কলকাতায় থাকবে?”
“আজ্ঞে না, কাল আমাদের খেলা রয়েছে, আজই আমাকে শক্তিগড়ে ফিরে যেতে হবে।”
“বেশ তো, তা-ই যেয়ো। কিন্তু দুপুরের ট্রেনেই যে ফিরতে হবে, তার তো কোনও মানে নেই। খেয়ে-দেয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে তারপর বিকেলের ট্রেন ধরলেই চলবে।… ওরে কৌশিক, তোর মাকে বল যে, ভুতোবাবু দুপুরে এখানেই খাবে। আর হ্যাঁ, ল্যাংচার হাঁড়িটা ভিতরে নিয়ে যা।”
কিন্তু কৌশিককে আর উঠতে হল না, একটা ট্রের উপরে মিষ্টি আর চায়ের কাপ নিয়ে পার্বতী ইতিমধ্যে ড্রয়িং রুমে এসে ঢুকেছিল। ট্রেটা সেন্টার টেবিলে নামিয়ে রেখে মেঝে থেকে মিষ্টির হাঁড়ি তুলে নিয়ে সে জানাল যে, একটু বাদেই আমাদের খেতে বসার ডাক পড়বে। ভাদুড়িমশাই বললেন, “মা’কে বলে দে, এই দাদাবাবুটিও দুপুরে আমাদের সঙ্গে খাবেন।”
ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে পার্বতী বলল, “মা’কে কিছু বলতে হবেনি মামাবাবু, সব দিকে তেনার নজর থাকে।”
ভূতনাথ অবশ্য দুপুরের খাওয়াটা এখান থেকে খেয়ে যেতে রাজি হল না। চা জলখাবার খেয়েই সে উঠে পড়ল। বলল, মানিকতলায় তার এক মাসির বাড়ি, তাকে বলা আছে যে, দুপুরে সে ওখানেই খাবে।
ভাদুড়িমশাই বললেন, “ঠিক আছে, কিন্তু আমার পক্ষে তোমাদের টুর্নামেন্টের খেলা দেখতে যাওয়া সম্ভব হবে কি না, সেটা তা হলে কী করে জানাব? এদিকে যে-সব কাজ জমে রয়েছে, তার একটা বিলিবন্দোবস্ত না করে তো যেতে পারছি না। তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব কী করে?”
“আপনি কেন যোগাযোগ করবেন,” ভূতনাথ হেসে বলল, “আপনাকে কিছু করতে হবে না। যেতে আদৌ পারবেন কি না, সেটা আপনি কখন বুঝতে পারবেন?”
“বিকেলের মধ্যেই বুঝে যাব।”
“ঠিক আছে, বড়-জ্যাঠামশাই তা হলে আজ রাত্তিরে… এই ধরুন নটা-দশটা নাগাদ আপনাকে ফোন করে সব জেনে নেবেন।”
“কৃপানাথ কোত্থেকে ফোন করবে?”
“কেন, আমাদের বাড়ি থেকে। গত বছরেই আমাদের বাড়িতে ফোন এসে গেছে।”
কথা শেষ করে ভূতনাথ আর দাঁড়াল না। ভাদুড়িমশাইকে প্রণাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।
এতক্ষণ আমরা সবাই চুপ করেছিলুম। কথাবার্তা যা হবার, তা ভাদুড়িমশাই আর ভূতনাথের মধ্যেই হচ্ছিল। সদানন্দবাবুর কৌতূহলই সবচেয়ে বেশি, তাই তিনিই প্রথম মুখ খুললেন। “কৃপানাথবাবু কে মশাই?”
“বর্ধমানের বিখ্যাত ডাক্তার।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “লোকে বলে বর্ধমানের বিধান রায়। কৃপানাথের পৈতৃক বাড়ি অবশ্য বর্ধমান শহরে নয়, শক্তিগড়ে। সেখান থেকে রোজ দু’ বেলা বর্ধমানের খোসবাগানে ওর চেম্বারে গিয়ে বসে। দুর্দান্ত প্র্যাকটিস, দম ফেলার ফুরসত নেই। এদিকে আবার তারই মধ্যে এই ফুটবল টুর্নামেন্টের ঝক্কি সামলাতে হচ্ছে। অথচ বয়েস তো নেহাত কম হল না!”
বললুম, “আপনার বন্ধু?”
“ছেলেবেলার… মানে সেই যখন কলেজে পড়তুম তখনকার বন্ধু। ভাদুড়িমশাই বললেন, “আই এসসির দুটো বছর একসঙ্গে পড়েছি। আই এসসি পাস করে ও গিয়ে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হয়। কিন্তু কলেজ আলাদা হলে কী হবে, কলেজ স্ট্রিটের বসন্ত কেবিন আর মির্জাপুর স্ট্রিটের ফেভারিট কেবিনে তখনও রোজ আড্ডা দিয়েছি। ময়দানে গিয়ে ফুটবল খেলাও দেখেছি একসঙ্গে। তারপরে যা হয় আর কি, ডাক্তারি পাস করে ও চলে গেল শক্তিগড়ে, তারপর পশার একটু জমে উঠতে বর্ধমানে গিয়ে চেম্বার খুলল। বাস্, “আমরা দুজনে দুই কাননের পাখি।”
সদানন্দবাবু বললেন, “দ্যাকাসাক্ষাৎ হয়?”
“কালেভদ্রে। শেষ দেখা হয়েছিল নাইনটিন সিক্সটি সেভেনের অক্টোবরে। ওদের শক্তিগড়ের বাড়িতে সেবারে একটা উইকএন্ড কাটিয়ে আসি।”
একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন ভাদুড়িমশাই। তারপর বললেন, “আঃ, সে-দুটো দিনের কথা এখনও ভুলিনি। পুকুরে মাছ ধরা হল, চড়ুইভাতি করা হল, গানে গল্পে ছুটির দুটো দিন যে কোথা দিয়ে কেটে গেল, টেরই পেলুম না।”
আবার একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন ভাদুড়িমশাই। বুঝলুম, স্মৃতি রোমন্থন করছে। খানিক বাদে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, “কৃপানাথের ছোটভাই বিশ্বনাথের কথা হচ্ছিল না? বিশ্বনাথের খেলা সেবারেই দেখি।”
অরুণ সান্যাল বললেন, “একটু আগে আপনি যা বলছিলেন, তাতে তো মনে হয় দুর্ধর্ষ স্ট্রাইকার ছিলেন। সত্যি?”
“ষোলো আনার উপরে আঠারো আনা সত্যি।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “আমি একটুও বাড়িয়ে বলিনি অরুণ। উনিশ বছরের ছেলেটা দেখলম চুনির মতন ঝটকা দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, আবার শুটিং পাওয়ারও প্রদীপের মতো। তা ছাড়া দরকারমতো নিজের স্পিড যেভাবে বাড়িয়ে কমিয়ে খেলছিল, আসলে সেটাই চিনিয়ে দিচ্ছিল ওর জাত। বুঝতে পারছিলাম যে, ফুটবলটা ওর রক্তের মধ্যে রয়েছে।”
কৌশিক দেখলুম মুখ টিপে হাসছে। বললুম, “হাসছ যে? বড়মামার কথা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?”
“না না, বিশ্বাস হবে না কেন?” কৌশিক বলল, “তবে কিনা আমি একটা অন্য কথা ভাবছিলুম। মানে একটু আগেই বোস-জেঠুর কাছে আমরা নসিপুরের হালা বাঁড়ুজ্যের গপ্পো শুনেছি তো, তাই ভাবছিলুম যে, শক্তিগড়ের বিশ্বনাথ দত্তও কি সেই গোত্রের খেলোয়াড়।”
শুনে সদানন্দবাবু হাঁ করে ঝাড়া এক মিনিট কৌশিকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, “সেই গোত্রের মানে?”
“মানে হালা বাঁড়ুজ্যে তো আর নিজে খেলতেন না, ভূতেরা তাঁর হয়ে খেলে যেত। তা শক্তিগড়ের বিশ্বনাথ দত্তের হয়েও কি তেনারাই খেলতেন নাকি?”
কৌশিকের কথা শুনে ভাদুড়িমশাই হোহো করে হেসে উঠলেন। তারপর হাসি থামিয়ে বললেন, “না রে কৌশিক, আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না। বুঝতে পারছি, চুনি আর প্রদীপের সঙ্গে তুলনা টেনেছি বলে তুই চটে গেছিস, কিন্তু যেমন চুনি তেমনি প্রদীপকেও তো আমি ভালই চিনি, তাই হলফ করে বলতে পারি যে, বিশ্বনাথের খেলা দেখলে ওরা কিন্তু একটুও চটত না, বরং মফসল থেকে ছেলেটাকে যাতে কলকাতার ময়দানে নিয়ে আসা যায় তার চেষ্টা করত।”
কৌশিক বলল, “সে-চেষ্টা কেউ কখনও করেনি?”
“করেছে বই কী।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “কৃপানাথের কাছে শুনেছি, কলকাতার অন্তত একটা বড় ক্লাব ওকে এখানে নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিল।”
“মোহনবাগান?’
“ওই তো তোদের মুশকিল, বড় ক্লাব বলতে তোরা আজকাল শুধু মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলকেই চিনিস। কিন্তু এ হল ত্রিশ বছর আগেকার কথা। তখন ফুটবলের মাঠে ইস্টার্ন রেলেরও দাপট নেহাত কম ছিল না। প্রদীপ মানে পি কে বরাবর কোথায় খেলত জানিস? মোহনবাগানেও না,ইস্টবেঙ্গলেও না, ওইইস্টার্ন রেলে। তোইস্টার্ন রেলেরই এক কর্তা—যদুর মনে পড়ছে, কে দাশ-ওকে চাকরি দিয়ে কলকাতায় নিয়ে আসার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কেন যে বিশ্বনাথের কলকাতায় আসা হল না, তাও তো একটু আগেই বলেছি। আসলে কৃপানাথের বাবাই তার এই ছোট ছেলেটিকে কলকাতায় আসতে দিলেন না।”
অরুণ সান্যাল বললেন, “সে একপক্ষে ভালই হয়েছে। ময়দানের নানা নোংরামির খবর আজকাল কাগজে খুব বড়বড় টাইপে ছাপা হচ্ছে। কিন্তু ভাবের ঘরে চুরি করে তো কোনও লাভ নেই, নোংরামিটা নেহাত গত দু-চার বছরের ব্যাপার নয়, ওটা আগেও অল্পবিস্তর ছিল। যেমন এখন রয়েছে, তেমনি সেভেন্টিজেও ছিল। বিশ্বনাথ দত্ত তখন যদি কলকাতায় খেলতে আসনে তো সেই নোংরা কাদার একটু-আধটু ছিটে কি আর তারও গায়ে লাগত না?”
আমি বললাম, “অরুণ, তুমি ভুল বলোনি। তবে কিনা নোংরামি তখনও ছিল বটে, কিন্তু আজকের মতন এতটা ছিল না। তা ছাড়া নোংরামির চরিত্রও যে ইতিমধ্যে পালটেছে, সেটাও খেয়াল করো। স্পিড আর স্ট্যামিনা বাড়াবার জন্যে খেলোয়াড়রা ওই যে কী সব গোলমেলে ট্যাবলেট খেয়ে মাঠে নামছে বলে শুনতে পাই, এরকম কথা কি আগে কখনও শোনা যেত?”
অরুণ সান্যাল বললেন, “কিন্তু ও-সব যারা খায়, খানিকক্ষণের জন্যে আর্টিফিশিয়ালি ওতে করে কিছুটা সুবিধে হয় ঠিকই, কিন্তু আলটিমেটলি তো স্বাস্থ্যের একেবারে বারোটা বেজে যায়, কিরণদা। আর তা ছাড়া ড্রাগ-অ্যাডিক্ট হয়ে পড়ারও তো একটা ভয় রয়েছে। বঁড়শিতে একবার আটকে গেলেই তো সর্বনাশ!”
“সে তো ঠিকই,” ভাদুড়িমশাই বললেন, “মারাদোনার যা হয়েছিল আর কী। অত বড় খেলোয়াড়, কিন্তু ওয়ার্ড কাপে ইউরিন টেস্টে ধরা পড়ল যে, ডোপ করে মাঠে নেমেছে। তখন তো বেইজ্জতির একশেষ!”
সদানন্দবাবু বললেন, “আরে ছা ছ্যা, কৌশিক আবার এর সুখ্যাত করছিল! আরে বাবা, খেলতে নেবেছিস তো নিজের জোরে খেলে যা! সেই যেমন শিবে ভাদুড়ি আর বিজয় ভাদুড়ি খেলত, সামাদ খেলত, লক্ষ্মীনারায়ণ আর মুর্গেশ খেলত! তা নয়, তোরা কিনা নেশা করে মাঠে নাবছিস? আরে ছ্যা ছ্যা, এ-রকম নোংরামির কথা কি আগে কখনও ভাবা যেত?”
অরুণ সান্যাল বললেন, “শুধু খেলোয়াড়দের দোষ দিযেই বা লাভ কী, সাপোর্টাররাও সব তেমনি হয়েছে! কী না, আমি যার সাপোর্টার, সব খেলাতেই তাকে জিততে হবে, একটা খেলাতেও তার হারা চলবে না! আরে মশাই, তা-ই কখনও হয়? এ তো খুবই সহজ কথা, কিন্তু শুনছে কে? হারলেই মারদাঙ্গা লাগিয়ে দেব, দল বেঁধে মাঠে নেমে খেলা ভণ্ডুল করে ছাড়ব, তারপর মাঠের বাইরেও দক্ষযজ্ঞ বাধিয়ে দিতে ছাড়ব না।”
“দক্ষযজ্ঞ বলতে পারো, লঙ্কাকাণ্ডও বলতে পারো,” ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, “সাপোর্টারদের যা-সব স্যা ‘দেখছি, তাতে তো মনে হয়, প্যান্টুল খুললেই অনেকের ন্যাজ বেরিয়ে পড়বে!”
কৌশিক বলল, “শুধু কলকাতার সাপোর্টারদের দোষ দিচ্ছ কেন, ইংরেজ সাপোর্টারদের তুলনায় তো এরা পারফেক্ট ভদ্দরলোক। ইংল্যান্ড যখন অন্য দেশে খেলতে যায়, এই সাপোর্টাররা তখন সেখানে গিয়ে যা-সব কাণ্ড করে, তা আর কহতব্য নয়। সেই জন্যে তো ওদের বাইরে যাওয়াই বন্ধ করে দিতে হয়েছে।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে তো ইংরেজদের নকল করার ঝোঁক ক্রমেই বাড়ছে। আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ তো দেখি ইংরেজদের চেয়েও বেশি ইংরেজ! তা এবাবে খেলার মাঠে বাঁদরামির ব্যাপারেও বোধহয় ওদের আমরা ছাড়িয়ে যাব।”
আমি বললুম, “মফসসলের খেলা কিন্তু আমাদের এই কলকাতার তুলনায় অনেক ভাল। গ্রামের পুজোয় যেমন একটা শান্ত ভদ্র চেহারা এখনও চোখে পড়ে, মফস্সলের ছোটখাটো গাঁ-গঞ্জেও তেমনি দেখবেন শহরের খেলার মাঠের এই উচ্ছল ব্যাপারটা এখনও ঢোকেনি।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “বেশ তো, তা হলে আমার সঙ্গে চলুন।”
“তার মানে?”
“কৃপানাথের চিঠিখানা পড়ুন, ভাদুড়িমশাই ঠোঁট টিপে হেসে বললেন, “মানেটা তা হলেই বুঝতে পারবেন।” বলে, ভূতনাথ তার বড়-জ্যাঠামশাইয়ের যে চিঠিখানা ভাদুড়িমশাইয়ের হাতে তুলে দিয়েছিল, সেন্টার টেবিল থেকে সেটা তুলে তিনি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। চিঠিখানা এখানে তুলে দিচ্ছি :
ভাই চারু,
সেই যে বছর ত্রিশ আগে তুমি আমাদের শক্তিগড়ের গ্রামের বাড়িতে একবার এসেছিলে, তারপরে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে মোটরযোগে যাতায়াতের পথে বার কয়েক বর্ধমানে আমার চেম্বারে এসে দেখা করে গিয়েছ বটে, কিন্তু গ্রামের বাড়িতে আর-কখনও আসোনি। অথচ যখনই দেখা হয়, তখন তো বটেই, চিঠিতেও বহুবার তুমি জানিয়েছ যে, শক্তিগড়ের বাড়ির সেই মধুর স্মৃতি তোমার চিত্তে এখনও অম্লান, এবং আবার তুমি সেখানে এসে কয়েকটা দিন কাটিয়ে যেতে চাও। কিন্তু কাজের চাপে কিছুতেই তোমার আসা হয় না।
কিন্তু ভাই, এবারে আর কাজের অজুহাত দিয়ো না। আজ রবিবার। আর ক’টা দিন বাদে সামনের উইকএন্ডটা এখানে এসে কাটিয়ে যাও। শনিবারের বদলে যদি শুক্রবার সকালে ট্রেনে অথবা মোটরযোগে এখানে পৌঁছে যাও তো আরও ভাল। তা হলে বিশ্বনাথের নামে আমরা এখানে যে ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করেছি, তার সেমিফাইনাল ও ফাইনালের খেলা তুমি দেখতে পাবে। ফাইনাল হচ্ছে রবিবার বিকেলে। তুমি প্রিসাইড করবে ও পুরস্কার বিতরণ করবে।
শক্তিগড় এখন আর সেই শক্তিগড় নেই, তুমি ভালই জানেনা। তবে আমাদের পুকুরটা আছে। তাতে মাছও আছে প্রচুর। শনিবারে খেলা থাকবে না, সেদিন ছিপ ফেলে মনের আনন্দে মাছ ধরতে পারবে।
এসো ভাই, নইলে আমার মুখরক্ষা হবে না। ইতি :
কৃপানাথ।
পুনশ্চ। বাঙ্গালোরে ফোন করে জানলাম যে, তুমি এখন কলকাতায়।
কাঁকুরগাছির ফ্ল্যাটের ঠিকানা তাঁরাই দিয়েছেন।–কৃপা
চিঠিখানা জোরে-জোরে পড়ে শোনাতে হল, যাতে সবাই শুনতে পান। পড়া শেষ হয়ে যাবার পরে সদানন্দবাবু বললেন, “আজ হল গে রোববার, ৬ এপ্রিল। তার মানে শুক্রবার হল ১১ এপ্রিল। তিনটে দিন… মানে এগারো, বারো আর তেরোই এপ্রিল শক্তিগড়ে কাটিয়ে চোদ্দো তারিখ সোমবার সকালে কলকাতায় ফিরে আপিস করা যাচ্চে। মন্দ কী!”
কৌশিক বলল, “আপনি তো রিটায়ার্ড ম্যান বোস-জেই, আপনার আবার আপিস কিসের?”
“আরে বাবা, আমি কি আর আমার কতা ভাবছিলুম?”
আমি বললুম, “সম্ভবত আমার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু নেমন্তন্নটা তো আপনারও নয়, আমারও নয়, ভাদুড়িমশাইয়ের। আপনার-আমার যাবার কথা অতএব উঠছেই না।”
“আরে না না, আমি একা যাব কেন?” ভাদুড়িমশাই বললেন, “যদি যাই তো সবাই মিলেই যাওয়া হবে। কী রে কৌশিক, যাবি?”
“অসম্ভব।” কৌশিক বলল, “টিকিট কাটা হয়ে গেছে, রিজার্ভেশন কনফার্ড, বুধবারে আমি বাঙ্গালোরে ফিরছি। আমার যাওয়ার কোনও কথাই উঠছে না।”
“কিরণবাবু, আপনি?”
“গেলে তো ভালই হয়।” আমি বললুম, “দিব্যি একটা আউটিং হয়ে যায়। ফাইভ-ডে উইকের শনি আর রবি তো ছুটি, বাকি রইল শুক্রবার। ও একটা দিন ক্যাজুয়াল নিয়ে নেব।”
“সদানন্দবাবু?”
“আমি তো যাবার জন্যে এক পা তুলে রেডি হয়েই আছি।” সদানন্দবাবু বললেন, “তা যাব কিসে? হাওড়া থেকে লোকাল ট্রেনে, না বাড়ি থেকে টানা মোটরগাড়িতে?”
“গাড়িতেই যাব। সকাল ছ’টা নাগাদ বেরিয়ে পড়ব, লেবেল ক্রসিংয়ে যদি আটকে না যাই তো শক্তিগড়ে পৌঁছতে দু’ঘণ্টার বেশি লাগবে না।”
পার্বতী এসে বলল, “মা বললেন, টেবিলে খাবার দেওয়া হয়ে গেছে, আপনারা এসে বসে পড়ুন।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “হ্যাঁ রে পার্বতী, যে ছেলেটা দেখা করতে এসেছিল, তোকে যখন তার নাম বলতে বললুম, তখা তুই বললি, “সে আমি বলতে পারবনি। তার মানে তোর স্বামীর নাম নিশ্চয় ভূতনাথ। তাই না?”
শুনে, মুখ নিচু করে পার্বতী যেভাবে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল, তাতে বুঝলুম, ভাদুড়িমশাই ব্যাপারটা ঠিকই আঁচ করেছেন।
টেবিলে খেতে বসে শক্তিগড়ে যাওয়ার ব্যাপারে আর কোনও কথা হল না। খাওয়া শেষ হবার পরে ড্রয়িংরুমে ফিরে এসে বললুম, “আচ্ছা, ফুটবল টুর্নামেন্টটা বিশ্বনাথ দত্তের নামে হচ্ছে কেন? উনি কি…”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “হ্যাঁ, বেঁচে নেই। পনরো বছর আগে মারা গেছে। ভূতনাথ তখন নেহাতই বাচ্চা। বাবার কথা ওর কিছু মনে নেই।
.
॥ ৩ ॥
রবিবার রাত দশটা নাগাদ কৃপানাথ দত্তের ফোন আসতে ভাদুড়িমশাই তাকে জানিয়ে দেন যে, আমরা মোট তিনজন তার ওখানে যাচ্ছি। শুক্রবার সকাল আটটা নাগাদই যে আমরা গাড়িতে করে শক্তিগড়ে পৌঁছচ্ছি, তাও তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়। তাতে তিনি বলেন যে, শক্তিগড়ে ঢুকে খানিকটা এগোলে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের বাঁ দিকে হেম ঘোষের মিষ্টির দোকানে ভূনাথ আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে।
তা আজ ১১ এপ্রিল শুক্রবার সকালে শক্তিগড়ে ঢুকে দেখলুম যে, ভূতনাথ সত্যিই আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে। তবে আটটা নয়, পোঁছতে পৌঁছতে পৌনে ন’টা বেজে যায়। কৃপানাথ দত্তদের বাড়ি অবশ্য ঠিক শক্তিগড়ে নয়; মুখে তারা শক্তিগড়ের কথাই বলেন বটে, কিন্তু বাড়িটা আসলে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড ছেড়ে খানিকটা ভিতরে ঢুকে এমন একটা এলাকায়, যেখানে পাকা বাড়ি গোটাকয় আছে ঠিকই, কিন্তু কাঁচা বাড়ির সংখ্যা সেই তুলনায় অনেক বেশি। রাস্তাটা অবশ্য কঁচা নয়, পিচের না-হলেও খোয়া-পেটানো।
দত্তদের বাড়িটা যে অনেক কালের, চেহারা দেখলেই সেটা বোঝা যায়। দোতলা বাড়ি; সদর আর অন্দর দুটো মহলই মস্ত মাপের; প্রচুর ঘর, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে তার কোনওটাই নেহাত ছোট নয়; সেকালের বাড়ি বলে সিলিং রীতিমতো উঁচু, জানলা দরজাও বড় বড়, ফলে ঘরগুলিতে গুমোট কিংবা দম-আটকা ভাবের সৃষ্টি হয়নি। চুন সুরকির গাঁথনির মোটা দেওয়াল বলে ঘরগুলো বেশ ঠাণ্ডাও বটে। এখানে এসে পৌঁছবার সঙ্গে-সঙ্গেই যে এত সব ব্যাপার খেয়াল করেছিলুম, তা নয়। সবই আস্তে-আস্তে দেখি, আর যতই দেখি, ততই বুঝতে পারি যে, কৃপানাথ দত্ত কেন কষ্ট করে এখান থেকে রোজ বর্ধমানে যান, কেন বর্ধমান শহরেই স্থায়ীভাবে তিনি থেকে যান না। আসলে এই ধরনের বাড়ির মধ্যে এমন একটা মায়ার ভাব থাকে, মানুষ যাতে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে যায়।
আসার পথে মগরায় খানিকক্ষণের জন্যে দাঁড়াতে হয়েছিল। রাস্তার ধারের একটা দোকানে তখন চা-বিস্কুট খেয়ে নিয়েছি। এখানে এসে হাতমুখ ধুয়ে ফের জলখাবার খেতে হল। বাড়ির পাশে মস্ত দিঘি। অনেক কাল বাদে সাঁতরে চান করা হল সবাই মিলে। তারপর মধ্যাহ্নভোজ সেরে ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়েও নিয়েছি। ঘুম থেকে উঠেছি তিনটে নাগাদ। তারপর খেলা দেখতে গিয়েছিলুম। সুলতানপুর স্পোটিং আর পোড়াবাজার ইলেভেনের সেমিফাইনাল খেলা। তাতে সুলতানপুরকে পাঁচ গোলে হারিয়ে পোড়াবাজার একেবারে ড্যাং ড্যাং করে ফাইনালে উঠে গেল। অন্য দিকের সেমিফাইনালে পলাশডাঙা ফুটবল ক্লাবকে একেবারে শেষ মিনিটে একটা গোল দিয়ে শক্তিগড় ব্রাদার্স ফাইনালে উঠেছে। কাল শনিবার খেলা নেই। পরশু রবিবার ফাইনাল।
মফস্বলের গ্রামে-গঞ্জে এইসব টুর্নামেন্ট নেহাত কম উন্মাদনা জাগায় না। যেখানে খেলা, সেখানকার স্থানীয় লোক তো বটেই, তার আশপাশের সব এলাকা থেকেও প্রচুর লোক খেলা দেখতে আসে। শুনলুম খেলার মাঠে নোজই বেশ ভিড় হয়। আজও যে হয়েছিল, সে তো স্বচক্ষেই দেখলুম। সুলতানপুর স্পোটিং যে খুব দুর্বল দল, তা নয়, এই নক-আউট টুর্নামেন্টের ট্রোফি গত বছর তারাই পেয়েছিল। কিন্তু এবারে যে সেমিফাইনালে তাদের গোহার হারতে হল, তার একটা কারণ যদি হয় রেফারির দু’ দুটো ভুল সিদ্ধান্ত, তত অন্য কারণ পোড়াবাজার টিমের ফরোয়ার্ড লাইনের দুর্ধর্ষ দুই খেলোয়াড়, বিপক্ষের ডিফেন্সকে যারা ভেঙেচুরে একেবারে তছনছ করে দিচ্ছিল।
রাত্তিরে তাই নিয়ে কথা হচ্ছিল। খাওয়ার পাট একটু আগে মিটেছে; সদর বাড়ির দোতলায় পাশাপাশি দুটো ঘরে আমাদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হয়েছে; বিছানা পাতা, মশারি খাটানো, ভূতনাথের তদারকিতে সমস্ত কাজ সমাধা হয়েছে, এখন গিয়ে শুয়ে পড়লেই হয়। কিন্তু শুয়ে পড়ার ইচ্ছে কারও আছে বলে মনে হল না। আপাতত আমরা বারান্দার উপরে গোল হয়ে বসে গল্প করছি। দিব্যি ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে, সামনে পুকুর, তার জলের উপরে কোত্থেকে যেন আলো এসে পড়েছে, সব মিলিয়ে এমন একটা পরিবেশ, যাতে জেগে থাকতেই ভাল লাগে।
কৃপানাথ দত্ত বললেন, “বুঝলে হে চারু, বিশ্বনাথের নামে এই টুর্নামেন্ট চালু করেছি নাইন্টিটুতে, অথচ এর মধ্যে একবারও আমরা ট্রোফিটা ঘরে তুলতে পারিনি। এদিকে
আবার এবার নিয়ে পরপর তিন বার আমরা ফাইনালিস্ট। গত দু’ বছর অল্পের জন্যে ট্রোফি ফশকে যায়। এবারে কী হবে কে জানে।”
ভাদুড়িমশাই তালুতে জিভ ঠেকিয়ে চুকচুক করে আক্ষেপ প্রকাশ করে বললেন, “এবারেও বোধহয় ফসকে যাবে।”
“একথা কেন বলছ?”
“বলছি পোড়াবাজার টিমের ফরোয়ার্ড লাইনের খেলা দেখে।”
সদানন্দবাবু বললেন, “বিশেষ করে ও-দুটো ছোঁড়ার তো কোনও তুলনাই হয় না। ওরে বাপ রে বাপ, ওদের দেকে তা আমার লক্ষ্মীনারায়ণ আর মুর্গেশের কম্বিনেশনের কতা মনে পড়ে যাচ্ছিল। আর কিকের জোর যা দেকলুম, একেবারে পাগলির মতো।”
“লক্ষ্মীনারায়ণ-মুর্গেশের খেলা আমি দেখিনি,”ভাদুড়িমশাই বললেন, “পাগলিরও না, তবে সোমানা-আপ্পারাওয়ের খেলা তো দেখেছি। না হে কৃপানাথ, আজ ওরা যা খেলল, পরশু যদি তার অর্ধেকও খেলতে পারে তো তোমার… মানে শক্তিগড়ের নো চান্স।”
কৃপানাথ দত্ত একেই মুষড়ে ছিলেন, ভাদুড়িমশাইয়ের কথা শুনে আরও নেতিয়ে পড়লেন। সেই অবস্থাতেও, সম্ভবত নিজেই নিজেকে একটু সাহস জোগাবার জন্যে, মজ্জমান ব্যক্তি যে-ভাবে হাতের সামনে যা-কিছু পায়, তা-ই আঁকড়ে ধরে, সেইভাবে বললেন, “অবিশ্যি আমাদের টিমও মোটেই ফ্যালন নয়। ভুতোর… মানে বিশ্বনাথের ছেলের খেলা তো তুমি দ্যাখোনি, দেখলে বুঝতে পারতে যে, ওই রকমের বডি-ফিটনেস আর স্টামিনা না-ই থাক, স্রেফ ট্যালেন্ট আর ফুটবল-সেন্সের কথা যদি ওঠে, তো ভুতো ওদের চেয়ে একটুও পিছিয়ে নেই, বরং দু’কদম এগিয়ে আছে। কিন্তু মুশকিল কী জানো, পাওয়ার-টেনিসের মতো এ হল পাওয়ার-ফুটবলের যুগ। যার যত মাল-পাওয়ার, খেলার মাঠে তার তত দাপট।… নাঃ, ওই মা-ম্যান দুটোই পোড়াবাজারকে জিতিয়ে দেবে, এবারেও আমরা পারলুম না!”
বললুম, “এত হতাশ হচ্ছেন কেন? আজ ভাল খেলেছে বলেই যে পরশুও ওরা ভাল খেলবে, তার তো কোনও মানে নেই। আমাদের কলকাতা ময়দানের নামজাদা সব ফুটবলারদের দেখছেন তো, পরপর দুদিন ওরা কেউ ভাল খেলে না। আজ যদি বাঘের মতো খেলল, তো কাল হয়তো খেলবে শেয়ালের মতো। না না, আপনি এত দমে যাবেন না তো।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “ভূতোবাবুর কথা বলছিলে। ওর খেলা তো দেখিনি। ওদের সেমিফাইনালের খেলা কবে ছিল?”
“গত সোমবার। সেদিন একসট্রা টাইম খেলানো হয়েছিল। তাও খেলাটা ড্র থেকে যায়। ফলে পরও… মানে বুধবার আবার খেলতে হয়। সেদিনও ড্র হতে যাচ্ছিল, কিন্তু একসট্রা টাইমের তিন মিনিটের মাথায় ভূতো কী বলব, অলমোস্ট আনবিলিভেবলি– একটা গোল করে বসে। সেই গোল্ডেন গোলেই আমরা জিতে যাই।”
“গোলটাকে অবিশ্বাস্য বলছ কেন?”
“এইজন্যে বলছি যে, মাঠের যে-হাফে আমরা খেলছিলুম, সেখান থেকেই একটা গ্রু পাস ধরে নিয়ে বিপক্ষের পরপর পাঁচজনকে কাটিয়ে বল নিয়ে ভূতো ওদের বক্সের মধ্যে ঢুকে পড়ে, তারপর যেন ডান পায়ে শট নিতে যাচ্ছে, এইভাবে বাঁ দিকে ঝুঁকে পড়ে সেই অবস্থাতেই বাঁ পায়ে শট নেয়। গোলকিপারের কিছু করার ছিল না, কেননা, ভুতোর ওই বাঁ দিকে ঝোকা দেখেই সে কমিটেড হয়ে গিয়েছিল।”
বললুম, “গত ওয়র্লড কাপে আফ্রিকার একজন ফুটবলারকে এগেস্ট দ্য রান অব দ্য প্লে ওইভাবে একটা গোল করতে দেখেছি। সেও একেবারে একার চেষ্টায় গোল করা।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “রাইট। গোলটা টিভিতে আমিও দেখেছিলুম। ইন ফ্যাক্ট দ্যাট। ওয়াজ অ্যাডজাজড টু বি দ্য বেস্ট গোল অভ দ্য টুর্নামেন্ট।… কিন্তু সে-কথা থাক। ভুতোর কথা হচ্ছিল। ওর খেলা আমি দেখিনি, তবে ওর মতো বয়েসে ওর বাপ কেমন খেলত, তা তো জানি। বিশ্বনাথের ফুটবল-ট্যালেন্টের অর্ধেকও যদি ভূতোবাবু পেয়ে থাকে, তো বলব, দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তোমাদের হারতে হবে না, ইট ওন্ট বি আ ওয়ন সাইডেড অ্যাফেয়ার।”
কৃপানাথ বললেন, “আমি তো সেই ভরসাতেই রয়েছি, তবে বাইরে যে সেটা প্রকাশ করব, এমন সাহস পাচ্ছি না। তা ছাড়া এদিকে আবার আর-একটা ঝাট বেধেছে।”
“কিসের ঝঞ্ঝাট?”
“ঝঞ্ঝাট আমাদের ভুতোর মা অর্থাৎ ছোট বউমাকে নিয়ে।”
“এর মধ্যে আবার তিনি কী করে আসছেন?”
“আসছেন ভুতোর জন্যে।” কৃপানাথ একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন, “কে যেন তার কানে তুলে দিয়েছে যে, পোড়াবাজার টিমে দুটো জল্লাদ-মার্কা ছেলে আছে, ভুতো যদি খেলতে নামে তো তার ঠ্যাং না ভেঙে তারা ছাড়বে না।”
“তাই কী হয়েছে?”
“এই হয়েছে যে, বউমা কান্নাকাটি জুড়ে দিয়েছেন। তার ইচ্ছে নয় যে, ফাইনাল খেলায় ভূতোকে আমরা মাঠে নামাই।”
একটুক্ষণ থেমে রইলেন কৃপানাথ। তারপর বললেন, “আসলে ব্যাপারটা কী হয়েছে জানো, খেলার মাঠে বিশ্বনাথ একবার মাথায় খুব চোট পেয়েছিল, মাঠ থেকে সরাসরি ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। মারাত্মক ইনজুরি, কনকাশন হয়েছিল, বাঁচবার আশা ছিল না।”
“এটা কবেকার ব্যাপার?”
“বিশ্বনাথের বিয়ের পরের বছরের।” কৃপানাথ বললেন, “তারপরে আর বিশ্বনাথ মাঠে নামেনি। বউমারও সেই থেকে ফুটবলের ব্যাপারে একটা আতঙ্ক জন্মে গেছে। ছেলে ফুটবল খেলছে, এমনিতেই এটা তার পছন্দ নয়। তার উপরে যেই শুনেছেন যে, ভূতের ঠ্যাং ভাঙার জন্যে পোড়াবাজার টিম একেবারে তৈরি হয়ে রয়েছে, ব্যস, আর কথা নেই, সঙ্গে-সঙ্গে কান্না জুড়ে দিয়েছেন তিনি।”
সদানন্দবাবু অনেকক্ষণ কোনও কথা বলেননি। কিন্তু এবারে আর মুখ না-খুলে পারলেন না। বললেন, “বাঙালির যে কিছু হয় না, স্রেফ এইজন্যেই হয় না। আরে বাবা, কেল্লার গোরার বুটজুতোর লাথি খেয়ে ছেলের পা ভাঙতে পারে, অভিলাষ ঘোষের মা কি তা জানতেন না? নাকি দুখিরামবাবু জানতেন না যে, কিংকং-মার্কা সায়েবের কাঁচ থেকে বল কাড়তে গিয়ে তার ভাইপো ছোনে মজুমদারের মাথা ফাটতে পারে? কিন্তু অভিলাষ ঘোষের মা কি তার জন্যে কখনও কান্নাকাটি করেছেন, নাকি দুখিরামবাবু তার আদরের ভাইপোকে ঘরের মধ্যে আটকে রেকেচেন?… না না, ভূতনাথের মা’কে সবাই গিয়ে বলতে হবে যে, এটা কোনও কাজের কতা নয়, ভূতনাথকে খেলতে দিতে হবে প্রমাণ করতে হবে যে, বাঙালি লড়তেও ভয় পায় না, মরতেও ভয় পায় না। বাঙালি যদি আজ মরার ভয়ে লড়তে না চায়, বাঙালি যদি আজ লড়ার ভয়ে…”
“আরে দূর মশাই, সদানন্দবাবুকে বাধা দিয়ে আমি বললুম, “অত বাঙালি-বাঙালি করছেন কেন? পোড়াবাজার টিমের ছেলেগুলো কি বাঙালি নয়? তবে হ্যাঁ, ওদের বডি ফিটনেস যে তারিফ করার মতো, সেটা বলতেই হবে। ইন ফ্যাক্ট, আজকের খেলায় সুলতানপুর টিমের সঙ্গে ওটাই ওদের একটা মস্ত তফাত গড়ে দিয়েছিল।
“পরশুও দেবে!” কৃপানাথ বললেন, “তবে সুলতানপুরের মতো পাঁচ গোলে না হেরে যাই। ওইরকম গোহার হারলে আর মুখ দেখানো যাবে না।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “এখুনি হারের কথা উঠছে কেন? ভুতোবা খেলবে তো?”
“তা খেলবে। ছোট-বউমাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আমি রাজি করাতে পারব। কিন্তু একা ভুতেই বা কী করবে। ও দুটো ষণ্ডাকে একা সামলানো ওর কম নয়।”
“ও কেন সামলাবে।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “ওদের পিছনে আর-দু’জনকে লাগিয়ে রাখো, ভুতোবাবু যাতে নিজের খেলাটা খেলতে পারে।”
সদানন্দবাবু বললেন, “সেই সঙ্গে রেফারিকেও একটু টিপে দিন না!”
কৃপানাথ বললেন, “তার মানে?”
“মানে আর কী, সবই তো বোজেন, এই বাজারে সব জায়গাতেই যা হচ্ছে আর কী..আরে মশাই, খেলা শুরু হবার আগে রেফারিকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে…”
“আরে ছি ছি,” কৃপানাথ দাঁতে জিভ কেটে, দু হাতের বুড়ো আঙুল দুই কানের লতিতে ছুঁইয়ে বললেন, “ঘুষ দেবার কথা বলছেন তো? আরে রাম রাম, ও-সব চিন্তাকে মাথায় ঠাই দেবেন না মশাই!”
“কেন,” সদানন্দবাবু বললেন, “পরশুর খেলায় কি ধর্মপুর যুধিষ্ঠির এসে রেফারি হচ্চে নাকি?”
শুনে আমরা হাসলুম বটে, কিন্তু কৃপানাথ হাসলেন না। বললেন, “সরকারি ইঞ্জিনিয়ার মাখন শিকদারকে যদি চিনতেন তো এমন কথা আপনি বলতেন না বোসমশাই।”
“তার মানে?”
“মানে আর কিছুই নয়, পরশুর খেলা নডাক্ট করছে মাখন শিকদার, যার অনেস্টি একেবারে আনকোয়েশ্চেনেবল। যুধিষ্ঠির তো তাও একবার কায়দা করে একটা ডিজনেস্ট কাজ করেছিলেন…এই হত ইতি গজর কথাটা বলছি আর কি, কিন্তু মাখন শিকদার বোধহয় তাও কখনও করেনি।”
“বটে?”
“আজ্ঞে হ্যাঁ। বিশ্বেস না হয় তো যতীন ঘোষকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।”
“যতীন ঘোষ আবার কে?”
“একজন ঠিকেদার।” কৃপানাথ বললেন, “ঘুষ দিয়ে একটা ব্রিজ মেরামতির টেন্ডার বাগাবার তালে ছিল। তাও যে সত্যি-সত্যি ঘুষ দিয়েছিল, তা নয়, স্রেফ হাত কচলাতে কচলাতে মাখন শিকদারকে বলেছিল যে, কাজটা যদি পায় তা হলে শিকদার-মশাইয়ের বেকার শালাটিকে সে…। বাস, আর কিছু বলার দরকার হয়নি, ওই যে ইঙ্গিতটুকু করেছিল, ওরই জন্যে যতীন ঘোষ ব্ল্যাক লিস্টেড হয়ে যায়। গত দু বছরে লোকটা একটাও সরকারি কাজ পায়নি।… না না, ওকে কিছু বলতে গেলে হিতে বিপরীত হবে।”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “এমনিতেও ও-সব নোংরামির মধ্যে যাওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করি। লোকটি পাস-করা রেফারি তো?”
“অফ কোর্স।” কৃপানাথ বললেন, “তা নইলে ওকে দায়িত্ব দেব কেন?”
“ভাল কথা। কিন্তু শুধু পাসকরা রেফারি হলেই তো হয় না, ধাঁচটা কেমন?”
“তার মানে?”
“মানে জবরদস্ত লোক কি না।” ভাদুড়িমশাই মৃদু হেসে বললেন, “মানে… আরও পরিষ্কার করে বলছি… বেশ শক্ত হাতে খেলাটা কনডাক্ট করতে পারবে কি না।
“তা পারবে।” কৃপানাথ বললেন, “এর আগে কোয়ার্টার ফাইনালের একটা ম্যাচ কনডাক্ট করেছিল। একটা গোল নিয়ে হাঙ্গামা বাধার উপক্রম হয়েছিল সেদিন। গোলটা যারা খেয়েছিল, তাদের একজন স্টপার এগিয়ে এসে রেফারির ডিসিশান নিয়ে আপত্তি জানাতেই মাখন শিকদার তাকে লাল কার্ড দেখিয়ে দেয়।… না না, বেশ কড়া লোক।”
“ভাল কথা।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “এখন একটু ঘরে চলল, তোমার সঙ্গে আর দু একটা কথা সেরে নেওয়া দরকার।”
“এঁরা?” কৃপানাথ বললেন, “এঁরা কি এখানেই থাকবেন?”
“হ্যাঁ হ্যাঁ, এমন চমৎকার বাতাস এঁরা কোথায় পাবেন। বারান্দায় বসে এঁরা যেমন গল্প করছেন করুন, সেই ফাঁকে আমরাও আমাদের পুরনো দিনের স্মৃতি রোমন্থন করে নিই।”
কৃপানাথকে সঙ্গে নিয়ে ভাদুড়মশাই বারান্দা থেকে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। তবে তার উদ্দেশ্য যে শুধুই স্মৃতি রোমন্থন, তা আমার মনে হল না।
.
॥ ৪ ॥
আজ ১৩ এপ্রিল, রবিবার। বাংলা ১৩০৩ সনের আজই ছিল শেষ দিন। কাল থেকে নতুন বছর শুরু হবে। বাংলা নববর্ষে আগে ছুটি পাওয়া যেত না, আজকাল কিন্তু যাচ্ছে, তাই ফলকের দিনটাও দিব্যি এখানে কাটানো যেত, কিন্তু ভাদুড়িমশাই কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না, বলছেন, ওরে বাবা, তাই কখনও হয়? কেন হয় না, জিজ্ঞেস করতে বললেন, ‘মালতী একেবারে মাথার দিব্যি দিয়ে বলে দিয়েছে যে, নববর্ষের দিনটা এবারে ওদের সঙ্গে কাটাতে হবেই। কৌশিক তো বাঙ্গালোরে, এখন আমিও যদি পয়লা বৈশাখটা বাইরে কাটাই, তা হলে ও খুব দুঃখ পাবে।”
আর-একটা দিন যাতে থেকে যাই, তার জন্যে কৃপানাথ দত্ত গোড়ায়-গোড়ায় খুব ঝুলোবুলি করছিলেন ঠিকই, সেই সঙ্গে এ বাড়ির অনন্যরাও খুবই চাইছিল যে, কালকের দিনটাও এখানে থাকি, কিন্তু ভাদুড়িমশাই যখন বললেন, ছোট বোনের কাছে তা হলে কথার খেলাপ হয়ে যাবে, তখন আর কেউ আপত্তি করলেন না। ভূতনাথ অবশ্য কথা আদায় করে নিল যে, অক্টোবর মাসে পুজোর কটা দিন তাদের বাড়িতে এসে কাটিয়ে যেতে হবে। ভাদুড়িমশাই বললেন যে, সেই সময়ে যদি বাঙ্গালোরের আপিসে খুব বেশি কাজ পড়ে না যায়, একমাত্র তা হলেই তাঁর কলকাতায় আসা সম্ভব হবে, আর কলকাতায় যদি আসেন তো শক্তিগড়ে এসে তিনটে দিন কাটিয়ে যাবেন ঠিকই। আর আমাদের তো না আসার কোনও কথাই ওঠে না। পুজোর কলকাতা থেকে বেরিয়ে পড়তে পারলে তো আমরা বেঁচে যাই।
যা-ই হোক, কালকের দিনটা দুপুরে মাছ ধরে আর বিকেল থেকে রাত্তির অব্দি ব্রিজ খেলে দিব্যি কেটেছে। আর আজকের দিনটার কথা তো ভোলা যাবে না। দিনটা ছিল উত্তেজনায় ঠাসা, বিকেলে খেলার মাঠে যা কিনা একেবারে চরমে উঠে যায়। কৃপানাথ দত্ত টুর্নামেন্ট কমিটির প্রেসিডেন্ট, প্রথম থেকেই তিনি ভয়ে-ভয়ে ছিলেন যে, একটা হাঙ্গামা হয়তো বেধে যেতে পারে, আর যদি বাধে তো সেটা নেহাত খেলার মাঠে আটকে থাকবে না। পোড়াবাজার টিমের সঙ্গে যে তিনটে বাস ভর্তি করে তাদের শ’খানেক সাপোর্টারও খেলার মাঠে এসে পৌঁছেছে, এই খবর শুনে ভয়টা আরও বেড়ে যায়। তিনি অবশ্য কাল বিকেলেই নিজে থানায় গিয়ে দারোগাবাবুকে বলে এসেছেন যে, খেলার মাঠে তাকে উপস্থিত থাকতে হবেই, আর দারোগাবাবুও তাকে অভয় দিয়ে বলেছেন, ঘাবড়াবার কিছু নেই, পোড়াবাজার থেকে যারা আসছে, তারা যদি কিছুমাত্র গোলমাল করে তা হলে প্রথমে তিনি মাইল্ড লাঠিচার্জ করবেন, আর তাতে যদি কোনও কাজ না হয় তো ফায়ারিংয়ের অর্ডার দিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবেন না। কিন্তু কৃপানাথের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল, দরকার হলে দনান গুলি চালাব মশাই,’ দাবোগাবাবুর এই কথা শুনে আশ্বস্ত বোধ করবেন কী, তিনি আরও নার্ভাস হয়ে পড়েছেন।
খেলা শুরু হবার কথা কাটায়-কাঁটায় ঠিক তিনটের সময়। কিন্তু শুরু হতে বেশ কিছুটা দেরি হয়ে গেল। কেননা, তার আগে স্থানীয় ইস্কুলের প্রাইমারি সেকশনের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেমেয়েরা ব্যান্ড বাজাতে বাজাতে মাঠ প্রদক্ষিণ করেছে। এস. ডি. ও. সাহেব আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি; জাতি গঠনে খেলাধুলার গুরুত্ব ও খেলার মাঠে শান্তি রক্ষার প্রয়োজনীয়তা কতখানি সেটা ব্যাখ্যা করে তিনি বেশ ওজনদার একটি বক্তৃতা দিয়েছেন। স্থানীয় গ্রাম-পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্টও ভাষণ দিয়েছেন একটি। তাতে তিনি বলেছে যে, এককালে তিনিও খুব ফুটবল খেলতেন, তবে গত কয়েক বছর যাবৎ যেহেতু জনসেবার কাজেই তাকে অহোরাত্র ব্যক্ত থাকতে হচ্ছে, তাই ইদানীং আর খেলাধুলোর জন্যে সময় দিতে পারছেন না। ওলিম্পিকের আদর্শের কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে স্থানীয় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গেম-টিচার বললেন, হারজিতটা কোনও কথা নয়, এই যে খেলার মাঠের প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়েছে এতগুলি দল, এই যোগদানটাই হচ্ছে আসল কথা। তিনি হয়তো আরও কিছু বলতেন, কিন্তু খেলা শুরু না হওয়া পর্যন্ত এস.ডি.ও. সাহেব যেহেতু জরুরি একটা কাজ থাকা সত্ত্বেও এখান থেকে চলে যেতে পারছেন না, তাই গেম-টিচার ভদ্রলোকের পাঞ্জাবির ঝুল ধরে বার দুই-তিন হ্যাঁচকা টান মেরে তাকে মধ্যপথেই থামিয়ে দেওয়া হল।
এর পরে শুভেচ্ছা বিনিময় পর্ব। মাঠের একদিকে একটা চাঁদোয়া খাঁটিয়ে তার তলায় পর-পর গোটা কুড়ি চেয়ার পেতে তাতে অভ্যাগতদের বসানো হয়েছে। দুই দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে এবার আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি ও প্রধান অতিথির পরিচয় করিয়ে দেওয়া হবে। খেলোয়াড়রা মাঠের মাঝখানে মুখোমুখি দুই সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন। দুই টিমের কোচও দাঁড়িয়ে আছেন নিজের নিজের খেলোয়াড়দের পাশে। কৃপানাথবাবু এসে ভাদুড়িমশাই ও এস. ডি. ও. সাহেবকে সেখানে নিয়ে গেলেন। পরিচয়পর্ব সাঙ্গ হতে লাগল তা অন্তত মিনিট দশেক। আমরা দূর থেকে দেখলুম যে, ভাদুড়িমশাই ও এস. ডি. ও. সাহেব খেলোয়াড়দের প্রত্যেকের সঙ্গে করমর্দন করতে করতে একটি দু’টি কথা বলছেন। কোচ দু’জনকে তো ভাদুড়িমশাই জড়িয়ে ধরলেনও।
এই যে পরিচয়পর্ব আর শুভেচ্ছা বিনিময়, খেলার মাঠে এর দরকার আছে বই কী। এটা আসলে একটা প্রতাঁকের মতো। মৈত্রীর প্রতীক। যেন এই প্রতাঁকের মাধ্যমেই বলে দেওয়া হচ্ছে যে, এখন আমরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ঠিকই, কিন্তু আসলে আমরা সবাই পরস্পরের বন্ধু। তাই দয়া করে কেউ যেন কোনও গণ্ডগোল কোরো না, খেলাটাকে নির্বিঘ্নে শেষ হতে দাও। যেন, ফলাফল যা-ই হোক না কেন, কারও মনে কোনও তিক্ততার রেশ থেকে না যায়।
শুভেচ্ছা বিনিময়ের এই পর্বের সঙ্গে যেমন খেলোয়াড়দের, তেমন দু’দলের কোচকেও যে জড়িয়ে দেওয়া হল, এর পিছনে কার মাথা কাজ করেছে, জানি না। তবে যার মাথাই কাজ করে থাক, সেটা যে পাকা মাথা, তাতে সন্দেহ নেই। কথাটা এই জন্যে বলছি যে, কোচদের উশকানির জন্যেই অনেক সময় খেলার মাঠে হাঙ্গামা বেধে যায়। খেলা যখন চলছে, তখন মাঠের ধারে বসে এমনভাবে তাদের অনেকে গলা ফাটিয়ে খেলোয়াড়দের তাতাতে থাকেন যে, তাতেই বেড়ে যায় উত্তেজনা। এমন কোচও দেখেছি, একটু ধৈর্য ধরে যাঁরা বসে থাকতেও পারেন না, মাঠের ধার বরাবর দৌড়তে দৌড়তে যাঁরা চেঁচাতে থাকেন। মনে হল, খেলা শুরু হবার আগে ভাদুড়িমশাই ওই যে দুই টিমের দুই কোচকে অত আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, এতেও শান্তি রক্ষার কাজ হবে কিছুটা। আর যা-ই করুন, এর পরে আর ওঁরা নিজের নিজের টিমকে এমনভাবে উত্তেজিত করবেন না, যার ফলে একটা হাঙ্গামা লেগে যেতে পারে।
কার্যত অবশ্য দেখা গেল যে, স্থানীয় টিমের কোচটি চুপ করে বসে খেলা দেখছেন বটে, কিন্তু পোড়াবাজারের কোচটির ক্ষেত্রে ভদ্রতা করে কোনও লাভ হয়নি। সেমিফাইনাল খেলার দিনে সুলতানপুরের বিরুদ্ধে তার খেলোয়াড়দের, বিশেষ করে ফরোয়ার্ড লাইনের সেই দুর্ধর্ষ খেলোয়াড় দুটিকে যেভাবে তিনি উশকে দিয়েছিলেন, আজও সেইভাবে উশকে যাচ্ছেন।
ব্যাপারটা মাঝে-মাঝে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তবু যে কোনও বড় রকমের গণ্ডগোল ঘটছিল না, তার দুটো কারণ। প্রথমত, মাখন শিকদার সত্যিই বেশ কড়া মেজাজের রেফারি। খেলা শুরু হবার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই দেখলুম, পিছন থেকে বিপজ্জনকভাবে ট্যাক্স করার জন্যে দু’ দলের দু’জন খেলোয়াড়কে তিনি হলুদ কার্ড দেখিয়ে দিলেন। তা ছাড়া, পোড়াবাজারের কোচটি হঠাৎ একবার তার একজন খেলোয়াড়কে বিকট চেঁচিয়ে কিছু নির্দেশ দিতেই রেফারি সঙ্গে-সঙ্গে খেলা থামিয়ে কোচটির কাছে এসে প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে বললেন, “যদি আপনার কাউকে কিছু বলার থাকে তো হাফ-টাইমে বলবেন; এখন যদি এইরকম যাঁড়ের মতন চেঁচান, তো মাঠের ধার থেকে আমি আপনাকে উঠিয়ে দেব।” কোচটির গলা তারপরে আর শোনা যায়নি। বোধহয় তিনি বুঝে গিয়েছিলেন যে, শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছেন, চেঁচামেচি করে এখানে বিশেষ সুবিধে হবে না।
পোড়াবাজার ফরোয়ার্ড লাইনের সেই ছেলে দু’টিকে সেমিফাইনাল খেলায় খুব লাফ ঝপ করতে দেখেছিলুম। পরস্পরের সঙ্গে ভাল রকমের বোঝাঁপড়া রয়েছে, দু’জনেই চমৎকার বল-প্লেয়ার, নিজেদের মধ্যে বল দেওয়া-নেওয়া করতে করতে এমন চমৎকারভাবে ওরা মাঝে-মাঝে আক্রমণে উঠে আসছিল যে, তাতেই চেনা যাচ্ছিল ওদের জাত। আক্রমণ আটকে যাবার পরে বল যখন আবার তাদের সীমানায় ফিরে যাচ্ছে, তখন ডিফেন্সে যাতে বড় রকমের কোনও ফঁক-ফোকর দেখা না দেয়, তার জন্য ওরা নেমেও যাচ্ছিল খুব তাড়াতাড়ি। দু’জনেরই দু’পা দেখলুম সমান চলে। সেটাও একটা মস্ত কারণ, যার জন্যে হঠাৎ-হঠাৎ জায়গা পালটে খেলতে ওদের কোনও অসুবিধে হচ্ছিল না। কিন্তু ওই যে বললুম, সেমিফাইনালের দিন ওরা যেরকম লাফ-ঝাঁপ করছিল, আর মাঝে-মাঝে একেবারে বুলডোজারের মতো ঢুকে পড়ছিল বিপক্ষের ব্যুহের মধ্যে, আজ সে রকম কিছু একবারও দেখতে পাইনি। শেষের দিকে এমনও মনে হচ্ছিল যে, ওদের দম ফুরিয়ে গেছে। দু’জনেরই দৌড়ের মধ্যে যে ভয়ংকর, প্রায় অবিশ্বাস্য রকমের, গতি সে দিন দেখেছিলুম, যতই ভাল খেলুক, সেই গতির অর্ধেকও আজ দেখতে পাচ্ছিলুম না।
বরং সেই তুলনায় ভূতনাথের খেলা দেখে তাক লেগে যাচ্ছিল আমাদের। সদানন্দবাবু সে-কথা বললেনও। “আরে মশাই, এ তো দেকচি মেওয়ালালের মতো খেলচে।” আমরা যেখানে বসে আছি, সেখান থেকে চেঁচিয়ে কাউকে সমর্থন করলে সেটা একটু অশোভন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সদানন্দবাবু যে তা জানেন না, তা নয়। কিন্তু ভূতনাথের খেলা দেখে তার মধ্যে যে আবেগ জমে উঠেছে, কতক্ষণ সেটাকে চাপা দিয়ে রাখবেন। তার চাপ সামলাতে না পেরে মাঝে-মাঝে, নিজের হাঁটু মনে করে, আমার হাঁটুতেই মস্ত এক-একটা চাপড় মেরে তিনি চেঁচিয়ে উঠছিলেন, “ওহোহোহো, এ কী খেলা খেলছিস রে ভূতত। চালিয়ে যা! চালিয়ে যা!”
ওদিকে, ফরওয়ার্ড লাইনের ছেলে দুটোর স্পিড কমে যাওয়ায়, আর তার ফলে পিছন থেকে যে-সব বল বাড়ানো হচ্ছে, চটপট জায়গামতো ছুটে গিয়ে সেগুলো ট্র্যাপ করতে না পারায়, পোড়াবাজারের আক্রমণ আজ ঠিক জমাট বাঁধতে পারছিল না। স্রেফ গতির অভাবেই তাদের মুভমেন্টগুলো শুরু হতে না হতেই ঝিমিয়ে যাচ্ছিল। আর তার সুযোগ নিচ্ছিল ভূতনাথের টিম। কৃপানাথ ভেবেছিলেন, পোড়াবাজারের বিরুদ্ধে তাদের টিম একেবারে দাঁড়াতেই পারবে না, সুলতানপুরের মতো তাদের কপালেও অশেষ দুর্ভোগ লেখা রয়েছে, তারাও পাঁচ-ছ গোলে হারবেন। কিন্তু আজ দেখা গেল, অত ভয় পাবার কিছু ছিল না, দক্ষতার বিচারে দুটো দলই আসলে সমান-সমান। কেউই কারও চাইতে বিশেষ এগিয়ে বা পিছিয়ে নেই।
লড়াইটাও তাই হাড্ডাহাড্ডি রকমের হচ্ছিল। দুই হাফ মিলিয়ে মোট নব্বই মিনিটের খেলা। তার অর্ধেক সময় কেটে গেছে, কিন্তু গোল হয়নি। পোড়াবাজারের মানিকজোড়ের একজন ইতিমধ্যে একটা সিটার’ নষ্ট করেছে। শক্তিগড় তেমন কোনও সহজ সুযোগ পায়নি। পাবার কথাও নয়। কেননা, আদৌ উঠে না গিয়ে যেভাবে তারা নিজেদের এলাকাতেই লোক বাড়িয়ে রেখেছে, তাতে মনে হচ্ছে আপাতত তাদের লক্ষ্য হচ্ছে গোল না খাওয়া।
হাফটাইমে দেখলুম পোড়াবাজারের কোচ হাত-পা নেড়ে বেশ উত্তেজিত ভঙ্গিতে তার টিমের ছেলেদের কিছু বলছেন। কৃপানাথ এতক্ষণ দোয়ার তলায় আমাদের সঙ্গে বসে খেলা দেখছিলেন। এস. ডি. ও. সাহেব যেহেতু বিরতির পরে আর থাকতে রাজি হলেন না, কৃপানাথ তাই তাকে তার জিপ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গেলেন। তাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে, দু’পক্ষের খেলোয়াড়দের বরফ আর কোল্ড ড্রিঙ্কস ঠিকমতো দেওয়া হয়েছে কি না, তার খোঁজখবর নিয়ে ফিরেও এলেন মিনিট পাঁচেকের মধ্যে। এসে বেজার মুখে বললেন, “একটা বড় বিচ্ছিরি ব্যাপার হয়েছে।”
বললুম, “এর মধ্যে আবার কী হল? কেউ জখম-টখম হয়নি তো?”
“না না, ইনজুরির ব্যাপার নয়।”
“তা হলে?” ভাদুড়িমশাই বললেন, “পোড়াবাজার থেকে বাস ভর্তি করে যে-সব সাপোর্টার এসেছে, তারা কোনও গণ্ডগোল বাধাবার তালে নেই তো?”
“আরে না, ওদের সাপোর্টাররা খুব ভালই জানে যে, গণ্ডগোল বাধিয়ে এখানে বিশেষ সুবিধে হবে না।”
“তা হলে?”
“আর বোলো না ভাই!” কৃপানাথ বললেন, “ওদের ওই কোচ ব্যাটাচ্ছেলে কী বলছে জানো?”
“কী বলছে?”
“বলছে যে, ওর পকেটমার হয়েছে! ভাবা যায়?”
“সে কী!” ভাদুড়িমশাই কিছু বলবার আগেই সদানন্দবাবু বললেন, “পকেটমার! সে তো কলকাতার ময়দানে বড় খেলার লাইন পড়লে হয় শুনেছি; আই. এফ. এ. ভার্সাস ইসলিংটন কোরিন্থিয়ানসের খেলার দিনে আমার মেজো মামাবাবুর যেমন হয়েছিল। টিকিট কাউন্টার অব্দি পৌচে দ্যাকেন যে, পকেট ফাঁক, ভিড়ের মদ্যে কে যেন তার মানিব্যাগ তুলে নিয়েছে, তাতে নগদ দশ আনা তিন পয়সা ছিল মশাই, সেটা হাপিস হয়ে যাওয়ায় মেজো মামাবাবুর আর টিকিট কেটে ভেতরে ঢোকা হল না, মাঠ থেকে শিকদারবাগান অলি হাঁটতে-হাঁটতে ফিরতে হল। কিন্তু সে তো কলকাতার পথেঘাটে হামেশাই ওসব হচ্ছে। বাট দিস ইজ নট ক্যালকাটা, এখানে কোত্থেকে পকেটমার আসবে।”
কৃপানাথ বললেন, “সেটাই হচ্ছে কথা! ব্যাটা আসলে এখানকার লোকদের এগেনস্টে একটা দুর্নাম রটিয়ে দেবার তালে রয়েছে। কিন্তু আমাদের লোক্যাল ছেলেরা যদি এটা টের পায়…মানে..”
কথাটা শেষ করতে গিয়েও শেষ করলেন না কৃপানাথ, এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বললেন, “সবই তো বোঝেন।”
সদানন্দবাবু একটা বিপদ ঠিকই আঁচ করেছিলেন, এটাও বুঝেছিলেন যে, কথাবার্তা এখন একটু নিচু গলায় হওয়াই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু বিপদটা যে কী হতে পারে, সেটাই ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কৃপানাথের দিকে একেবারে ভ্যাবলার মতো খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে তততধিক চাপা গলায় তিনি বললেন, “কী বুজব?”
ওদিকে ততক্ষণে সেকেন্ড হাফের খেলা শুরু হয়ে গেছে। সদানন্দবাবুর কথার উত্তর দিয়ে কৃপানাথ বললেন, “কাণ্ড দেখুন, আমাদের ছেলেগুলো তো একেবারেই অ্যাটাকে যাচ্ছে না। এদের হল কী! কোথায় ওদের এরিয়ার দখল নিবি, তা নয়, গুটিয়ে গিয়ে নিজেদের এরিয়ার মধ্যেই জট পাকিয়ে ঘুরছে।”
ভাদুড়িমশাই বলেলন, “এটা হয়তো ইচ্ছে করেই করছে।”
“কেন, কেন, ইচ্ছে করে করবে কেন,” সদানন্দবাবু বললেন, “ওরা…আই মিন পোড়াবাজার যেমন এদের গোল-এরিয়ায় এসে হানা দিচ্ছে, তেমনি এদেরও তো ওদের এরিয়ায় গিয়ে হামলা করা উচিত।”
সদানন্দবাবুর অনেক কথাতেই আমি সায় দিই না, কিন্তু এই কথাটায় দিতেই হল। ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললুম, “সদানন্দবাবু তো ভুল বলেননি। অলরেডি যে ওরা পাঁচ-পাঁচটা কর্নার পেয়েছে, সেটা খেয়াল করেছেন?”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “তা করেছি বই কী।”
“ওর যে-কোনও একটা থেকে গোল হয়ে যেতে পারত।
“কিন্তু হয়নি যে, সেটাই হচ্ছে আসল কথা।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “খেয়াল করে দেখুন, এতগুলো কর্নার পেয়েছে ওরা, সেই সঙ্গে গোল বক্সের একটু বাইরে থেকে দু দুটো ফ্রি-কিকও পেয়েছে, কিন্তু কোনওটা থেকেই কিছু ফয়দা তুলতে পারেনি। এদিকে আবার এই যে ওরা বার-বার এসে এদের গোলবক্সে হানা দিচ্ছে, এতে যে ওদের শক্তি ক্ষয় হচ্ছে, দম ফুরিয়ে আসছে, ফলে আক্রমণের ঝাঁঝও ক্রমেই কমে যাচ্ছে, সেটা তো কারও না বোঝার কথা নয়।”
কথাটা ভাদুড়িমশাই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন ঠিকই, তবে কিনা বললেন আসলে আমাদের সকলের উদ্দেশেই। কৃপানাথ তাঁর কথার পিঠে কিছু একটা মন্তব্য করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তিনি মুখ খুলবার আগেই বছর একুশ-বাইশের কালো, লম্বা, লোহা-পেটানো পেশল শরীরের একটি ছেলে এসে বলল, “জ্যাঠামশাই, আর তো সহ্য হচ্ছে না!”
কৃপানাথের মুখ দেখে মনে হল, তিনি ভয় পেয়ে গেছেন। শুকনো গলায় বললেন, “কেন, নতুন করে আবার কী হল?”
“ওদের কোচটা বলছে যে, যেখানে এলে পকেট মারা যায়, টিম নিয়ে সেই চোর ছ্যাচড়দের জায়গায় খেলতে আসাই উচিত হয়নি।”
“আহাহা, এতে এত রেগে যাচ্ছিস কেন?” ছেলেটিকে শান্ত করার ভঙ্গিতে কৃপানাথ বললেন, “সকলের সব কথা কি ধরতে আছে! আপন মনে তো কত জনে কত কথাই বলে, সে-সব কথা কানে না নিলেই হল!”
“আপন মনে বলেনি জ্যাঠামশাই! চেঁচিয়ে পাঁচজনকে শুনিয়ে বলছিল!”
“তুই নিজের কানে শুনেছিস?”
“আমি শুনিনি, তবে শঙ্কর আর ন্যাপাকে তো আমি ওর খুব কাছেই দাঁড় করিয়ে রেখেছিলাম, তারা শুনেছে। বলেন তো দু’ঘা লাগিয়ে দিই।”
“আরে না না,” কৃপানাথ শিউরে উঠে বললেন, “ও-সব করতে যাস না। বাইরের টিমের কোচের গায়ে আমরা হাত তুলেছি, এটা যদি রটে যায় তো কী হবে জানিস?”
“কী হবে?”
“বাইরে থেকে কোনও টিমই আর কখনও এই টুর্নামেন্টে খেলতে আসবে না। না না, যে যা-ই বলুক, তোরা বাবারা একটু শান্ত হয়ে থাক তো।”
“ঠিক আছে জ্যাঠামশাই,” ছেলেটি বলল, “আপনি যখন এত করে বলছেন, আমাদের ছেলেগুলোকে তখন সামলে রাখার চেষ্টা করছি। কিন্তু ফের যদি ও-লোকটা ওই রকমের কথা বলে, তা হলে কিন্তু আগুন জ্বলবে।”
সদানন্দবাবু যে ঘাবড়ে গেছেন, সে তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। ছেলেটি চলে যেতে সেই আগের মতো চাপা গলায় কৃপানাথবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন “কী ব্যাপার মশাই? সত্যি-সত্যি আগুন জ্বলবে নাকি?”
কিন্তু কৃপানাথবাবুর কাছ থেকে এবারেও কোনও স্পষ্ট উত্তর পাওয়া গেল না। এবারেও তিনি সেই আগের মতোই নিস্তেজ, নেতিয়ে পড়া গলায় বললেন, “সবই তো ববাঝেন।”
সদানন্দবাবুর খেলা দেখার উৎসাহ চলে গিয়েছিল। ভাদুড়িমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, “একটা কতা জিগেস করচি, কিছু মনে করবেন না, খেলাটা কি শেষ পর্যন্ত দেকতেই হবে?”
ভাদুড়িমশাই বললেন, “সে কী মশাই, এমন হাড্ডাহাড্ডি লড়াই, কে হারে কে জেতে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, এ-খেলা শেষ পর্যন্ত না দেখেই উঠে যাবেন?”
“না, মানে শরীরটা একটু খারাপ লাগছে কিনা, তাই ভাবছিলুম..”
“ভাববার কিছু নেই,” আমি বললাম, “নিশ্চিন্ত থাকুন, আগুন জ্বলবে না, ও-সব কথার কথা। আর তা ছাড়া খেলা তো প্রায় শেষ হয়ে এল, আর মাত্র দশ মিনিট।”
শুনে, সদানন্দবাবু কপালে হাত ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, “দুগা দুগ্ন, এই দশটা মিনিট এখন ভালয়-ভালয় কাটলে বাঁচি।”
আশ্চর্য কাণ্ড, ওই দশ মিনিটের মধ্যেই খেলাটা একেবারে দুম করে বদলে গেল। পোড়াবাজারের সেই মানিকজোড় নিজেদের মধ্যে বল দেওয়া-নেওয়া করতে করতে একটু বেশি রকমের বিপজ্জনকভাবে এসে পড়েছিল একেবারে শক্তিগড়ের বক্সের সামনে। সেখান থেকে তাদের মধ্যে একজন হঠাৎ বাঁ দিকের স্টপারকে কাটিয়ে গোলে শট নেয়। কিন্তু একে তো শক্তিগড়ের গোলকিপার আর ডান দিকের স্টপার ততক্ষণে জায়গামতো পজিশন নিয়ে গোলের মুখটাকে খুবই ছোট করে এনেছে তার উপরে আবার ফরোয়ার্ড লাইনের খেলোয়াড়টির খাটুনির চাপ ইতিমধ্যে বড্ড বেশি হয়ে যাওয়ায় তার শটে তেমন জোরও ছিল না। ভূতনাথ ওদিকে বক্সের কাছাকাছি একটু ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছিল। গড়ানে শটটিকে হাত দিয়ে তুলে নিয়ে গোলকিপার সেটিকে ভূতনাথের দিকে ছুঁড়ে দিতেই বলটিকে ট্র্যাপ করে ভূতনাথ পরক্ষণেই এমনভাবে ছুটতে শুরু করে যে, বুঝতে পারা যায়, এইরকম একটা সুযোগের প্রতীক্ষাতেই ছিল সে। পোড়াবাজারের গোলকিপার আর একজন স্টপার ছাড়া বাকি ন’জন খেলোয়াড়ই তখন শক্তিগড়ের গোলের দিকে উঠে এসেছে, বলতে গেলে বাদবাকি মাঠ একদম ফাঁকা। স্টপারটি তাকে আটকাতে এসেছিল, কিন্তু এক সেকেন্ডের জন্যে থেমে থেকে, হঠাৎই গতি বাড়িয়ে ভূতনাথ একেবারে ছিটকে বেরিয়ে যায় তার পাশ দিয়ে। গোলকিপার বিপদ বুঝে সামনে এগিয়ে এসেছিল ঠিকই, কিন্তু ভূতনাথ আর তাকে কাটাবার চেষ্টা না করে ডান পায়ের একটা ছোট্ট টোকায় বলটাকে তার মাথার উপর দিয়ে লব করে গোলে পাঠিয়ে দেয়।
শক্তিগড়ের বাসিন্দারা তো খেলা শুরু হবার ঘণ্টা খানেক আগে থেকেই দলে দলে মাঠে এসে জমায়েত হয়েছিলেন। সেই জমাটি ভিড়ের ভিতর থেকে পরক্ষণেই যে চিৎকারটা ওঠে, যদি শুনি যে, বর্ধমান শহর থেকেও সেটা শোনা গিয়েছিল তো অবাক হব না। সেটাই অবশ্য শেষ জয়ধ্বনি নয়। খেলা শেষ হতে তখনও আরও মিনিট ছয় সাত বাকি, তারই মধ্যে আরও দু-দুবার জয়ধ্বনি ওঠে। তিনটে গোলই ভূতোবাবুর। তার মধ্যে শেষ গোলটা এল বাইসিল কিক থেকে। আর সেটা আসার সঙ্গে-সঙ্গেই বেজে উঠল রেকারির হুইল। একবার নয়, দু’বার। একটা বাঁশি গোলের, অন্যটা খেলা শেষের।
খেলা শেষ। কিন্তু উত্তেজনা শেষ নয়। শক্তিগড়ের বাসিন্দারা তারস্বরে চেঁচাচ্ছেন, জনা কয়েক খেলোয়াড় ভুতোকে কাঁধে তুলে নিয়ে ঘুরছে, কৃপানাথের চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে, আর পোড়াবাজারের কোচটি তারই মধ্যে চেঁচিয়ে কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে, কিন্তু সেটা যে কী, চারপাশের তুমুল হট্টগোলের মধ্যে কথাগুলো চাপা পড়ে যাওয়ায় তা আর কেউ বুঝে উঠতে পারছে না।
সদানন্দবাবুর ভয় কেটে গিয়েছিল। উত্তেজনায় তিনি টগবগ করে ফুটছিলেন। ভূতনাথের খেলা দেখে তিনি এতই মুগ্ধ যে, পুরস্কার বিতরণের সময় তার নামে একটা মেডেল ডিক্লেয়ার করে দিলেন। বললেন, কলকাতায় গিয়ে আমাদের স্যাকরাকে দিয়ে রুপোর মেডেল বানিয়ে তাতে ভুতোবাবুর নাম খোদাই করে সামনের হপ্তার মধ্যেই পাঠিয়ে দেব।
মারা যাবার পরে সবাই যেমন সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করে, পুরস্কার বিতরণী সভাতেও সভাপতিরা তেমন ‘সময়োচিত বক্তৃতা দেন। ভাদুড়িমশাই একটি সময়োচিত বক্তৃতা দিলেন। খেলাধুলোর উপকারিতা সম্পর্কে দু’চার কথা বলার পরে বিশেষ করে আজকের ফাইনাল খেলা সম্পর্কে বললেন, “পোড়াবাজার বেশ শক্তিশালী দল, কিন্তু একই সঙ্গে একটু বেহিসেবি। নয়তো খেলার প্রথমার্ধে নিজেদের শক্তির চোদ্দো আনাই তারা খরচ করে ফেলত না। এই অপচয়ের মাসুলই তাদের দ্বিতীয়ার্ধে দিতে হয়েছে। শক্তিগড় সেক্ষেত্রে প্রথমার্ধে তাদের শক্তি-সামর্থ্যের ভাড়ার অটুট রেখে পোড়াবাজারের আক্রমণগুলিকে ঠেকিয়ে গিয়েছে মাত্র। দ্বিতীয়ার্ধেরও অনেকটা সময় তারা আক্রমণে ওঠেনি। উঠেছে একেবারে শেষ সময়ে, যখন সেই আক্রমণ ঠেকাবার মতো সামর্থ্য আর পোড়াবাজারের ছিল না। খেলার সঙ্গে যুদ্ধের তুলনা টেনে বলা যায়, এও আসলে এক ধরনের ওয়ার অব অ্যাট্রিশন। নিজের পুঁজি যতটা পারা যায় অটুট রেখে শত্রর পুঁজিকে শেষ করে আনা। শক্তিগড়ের এই যে কৌশল, এটাই তাদের সাফল্য এনে দিয়েছে।”
খেলার ফলাফল সম্পর্কে ভাদুড়িমশাইয়ের এই যে ব্যাখ্যা, এটা নিয়ে যে আমার মনে কোনও ধন্ধ ছিল না, তা নয়, কিন্তু তখন আর এ নিয়ে কিছু বললাম না। কথাটা তুললুম ঘণ্টা কয়েক বাদে। রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকে যাবার পর।
রেফারির শেষ হুইল বাজার পরে মাঠের মধ্যে যে জয়োল্লাসের সূচনা হয়, তার জের তখনও পুরোপুরি মেটেনি। ভূতনাথের গলায় যে গণ্ডা-দশেক পুষ্পমাল্য পরানো হয়েছে, তাতেই তার একেবারে ঢাকা পড়ে যাবার জোগাড়। সেই অবস্থায় একটা লরির উপরে বসিয়ে ভূতনাথ সমেত গোটা টিম নিয়ে সারা তল্লাট জুড়ে ঘোরা হয়েছে। হঠাৎ যে সেই লরিতে কেন সদানন্দবাবুকে তুলে দেওয়া হয়েছিল, ঈশ্বর জানেন; তবে ছেলেছোকরাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে তিনিও দেখলুম সমানে চেঁচাচ্ছেন : শিন্ড ফাইনাল জিতল কে, শক্তিগড় ইউনাইটেড আবার কে। বার কয়েক পাড়া প্রদক্ষিণ করে ছেলেছোকরার দল দত্তবাড়ির সামনে এসে জমায়েত হবার পরে তাদের মধ্যে ল্যাংচা বিতরণের পর্বও শেষ হয়েছে। এ-দিক ও-দিক থেকে তার পরেও যে জয়ধ্বনি উঠছে না, তা নয়, দু-চারটে বোমা-পটকাও ফাটছে মাঝে-মধ্যে, তবে খানিক আগের সেই মত্ত ভাবটা এখন আর নেই।
কৃপানাথের পরের ভাই শম্ভুনাথের উপরেই যেহেতু অতিথি-আপ্যায়ন ও ল্যাংচা বিতরণের দায়িত্ব ছিল, তাই এতক্ষণ তিনি দম ফেলবার ফুরসত পাচ্ছিলেন না। হই-হল্লা থেমে যাবার পরে রাত দশটা নাগাদ তিনি আমাদের কাছে এসে বললেন, “আপনারা তো কাল ভোরেই রওনা হচ্ছেন, তা হলে আর দেরি করা ঠিক হবে না, রাত্তিরের খাওয়া চুকিয়ে এবারে শুয়ে পড়াই ভাল।”
শুতে শুতে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই বারোটাই বাজল। তার আগে কালকের মতো আজও দোতলার বারান্দায় এসে বসেছি। হঠাৎ ভাদুড়িমশাই বললেন, “কী ব্যাপার বলুন তো কিরণবাবু, মনে হচ্ছে যেন কিছু একটা ব্যাপার নিয়ে আপনি খুব চিন্তায় পড়ে গেছেন।”
হেসে বললুম, “না না, তেমন কিছু না, তবে কিনা একটা ব্যাপার নিয়ে যে একটু ভাবছি, সেটা ঠিক। তাই নিয়ে একটু অস্বস্তিও হচ্ছে।”
“কী নিয়ে ভাবছেন?”
“আপনারই একটা কথা নিয়ে। মাঠে আপনার বক্তৃতায় আপনি বললেন যে, পোড়াবাজার টিমের তাবৎ শক্তি খেলার ফাস্ট হাফেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, তাই শেষ দিকে আর তারা কিছু করে উঠতে পারেনি। কিন্তু সত্যিই কি তা-ই?”
তা ছাড়া আর কী,” ভাদুড়িমশাই বললেন, “সেকেন্ড হাফের শেষ দিকে তো সেই জন্যেই ওরা শক্তিগড়ের ফরোয়ার্ড লাইনকে আটকাতে পারল না। ভীষণ হাপসে গেল যে!”
বললুম, “তা-ই যদি হবে তত সেমিফাইনালের দিনে দুই হাফেই পোড়াবাজার অত ভাল খেলল কী করে? নব্বই মিনিটের খেলা, তার প্রথম থেকে শেষ মিনিট পর্যন্ত ওরা একইরকম স্পিডে, একইরকম দাপটের সঙ্গে সেদিন খেলেছে। বিশেষ করে ওই মানিকজোড়। কই, ফাস্ট হাফে যে ওয়র্ক-লোড ওরা নিয়েছিল, তার জন্যে তো সেদিন সেকেন্ড হাফে ওরা একটুও হাপসে যায়নি। আজ তা হলে এমন হল কেন?”
ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, “আহা, বাইচং আর চিমাও কি রোজই ভাল খেলে নাকি। মাঝে-মাঝে কি ওরাও ঝিমিয়ে যায় না? ধরে নিন, পোড়াবাজারের ওই মানিকজোড়ও আজ ঠিক ফর্মে ছিল না, ফাস্ট হাফে ভাল খেললেও সেকেন্ড হাফে ঝিমিয়ে গিয়েছিল।
শুনে চুপ করে গেলুম বটে, কিন্তু ব্যাখ্যাটা খুব জুতসই বলে মনে হল না, অস্বস্তির একটা কাটা কোথাও বিধেই রইল। ভাদুড়িমশাইকে সে-কথা বললুমও। হেসে বললুম, “যা-ই বলুন মশাই, ধাঁধাটা কিন্তু কাটল না।”
.
॥ ৫॥
আজ ১৪ এপ্রিল সোমবার। ভোর ছ’টায় শক্তিগড় থেকে রওনা হয়ে সাড়ে আটটায় বালি ব্রিজ পেরিয়ে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছই। ভেবেছিলুম সাড়ে ন’টার মধ্যেই শেয়ালদায় আমাদের বাড়িতে পৌঁছে যাব। সেখানে আমাকে আর সদানন্দবাবুকে নামিয়ে দিয়ে ফ্লাইওভার পেরিয়ে ফের উত্তরমুখো হয়ে আপার সার্কুলার রোড ধরে ভাদুড়িমশাই কাকুরগাছিতে চলে যাবেন। কিন্তু আজ বাংলা নববর্ষ। ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা নানান জায়গায় মিছিল বার করেছে। ব্যান্ড পার্টিও বেরিয়েছে এখানে-ওখানে। ফলে ইতস্তত গাড়িঘোড়া আটকে গিয়ে জ্যামও নেহাত কম হচ্ছে না। দক্ষিণেশ্বর থেকে শেয়ালদা পৌঁছতে তাই পাক্কা দু ঘণ্টা লেগে গেল। দুপুরে একটু দেরি করে আপিসে গিয়েছিলাম। ফিরতে ফিরতে রাত ন’টা। তারপর গান করে, রাত্তিরের খাওয়া চুকিয়ে বসার ঘরে এসে একটা সিগারেট ধরিয়ে এখন একটু বিশ্রাম নিচ্ছি। নতুন একটা বই বেরোচ্ছে। পাবলিশার তার প্রুফ দিয়ে গেছে। একটু বাদে সেই পুফ নিয়ে বসব। তার আগে বরং যে ঘটনার কথা এখানে বলতে বসেছি, তার শেযটুকু বলে নিই।
কালকের শিল্ড ফাইনালে পোড়াবাজারের অত খারাপ খেলার যে ব্যাখ্যা ভাদুড়িমশাই দিয়েছিলেন, তা যে আমার মনঃপুত হয়নি, তা তো আগে বলেইছি। এও বলেছি যে, ভাদুড়িমশাই যা-ই বলুন, অস্বস্তির একটা কাটা আমার মনের মধ্যে তার পরেও বড্ড খচখচ করছিল। রাত্তিরে, ঘুমিয়ে পড়ার আগে, সদানন্দবাবুর সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছিল, অস্বস্তি একা আমার নয়, তারও। বিছানায় শুয়ে দু’চার বার এপাশ ও পাশ করে সদানন্দবাবু বললেন, “দেকুন মশাই, একটা কতা বলব?”
বললুম, “বলে ফেলুন।”
“আমরা তো এঁয়াদের গেস্ট, ঠিক কি না?”
“বিলক্ষণ।”
“এঁয়ারা আমাদের খুবই যত্ন-আত্তি করচেন, ঠিক কিনা?”
“সে আর বলতে?”
“পঞ্চব্যঞ্জনের বদলে পঞ্চান্ন ব্যঞ্জন খাওয়াচ্চেন বললেই ঠিক হয়, তাই না?”
“অবশ্য।”
“তার উপরে দেকুন, মুখ ফুটে কিছু বলবার আগেই এয়ারা স্পেশ্যাল অর্ডার দিয়ে তিন হাঁড়ি ল্যাংচা আনিয়ে রেকেচেন। কেন জানেন?”
“কেন?”
“কাল সকালে, আমাদের গাড়িতে তুলে দেবেন।”
“বলেন কী?”
“ঠিকই বলছি।” সদানন্দবাবু বললেন, “এবারে আপনি বেশ ভেবেচিন্তে একটা কতা বলুন তো।”
“কী বলব?”
“যারা আমাদের জন্যে এত করচেন, শিল্ড ফাইনালে এই যে তারা জিতলেন, এতে তো আমাদের খুশি হওয়াই উচিত, তাই না?..না না, তাড়াহুড়ো করতে হবে না, বেশ ভেবেচিন্তে বলুন।”
“এতে এত ভাববার কী আছে,” বললুম, “নিশ্চয় খুশি হওয়া উচিত।”
ঘর অন্ধকার। তবু বুঝলুম, সদানন্দবাবু একটা দীর্ঘ নিশাস মোচন করলেন। বললুম, “কী হল, চুপ করে গেলেন কেন?”
“কী আর বলব বলুন,” খুবই বিভ্রান্ত গলায় সদানন্দবাবু বললেন, “খুশি হওয়াই যে উচিত, তা কি আর আমি জানি না? জানি। কিন্তু হতে পাবচি কোতায়?”
“তার মানে?”
“মানে আর কিচুই নয়, ব্যাপারটা একটু ফিশি লাগছে।” এক সেকেন্ড চুপ কবে থেকে সদানন্দবাবু বললেন, “আপনার লাগছে না?”
“পোড়াবাজারের ওই ছেলে দুটোর কথা ভেবে এ-কথা বলছে তো?”
“এগজ্যাকটলি। পরও ওরা অত ভাল খেলেছিল। আজও ফাসঁ হাফে দাপিয়ে খেলেছে। অথচ তার পরেই কেমন যেন চুপসে গেল। কোনও মানে হয়?”
বললুম, “ভাদুড়িমশাই তো বললেন, ফার্স্ট হাফে অত দাপিয়ে খেলার জন্যেই সেকেণ্ড হাফে হাসে গেসল। তখন আর দম পায়নি।”
সদানন্দবাবু বললেন, “সে তো উনি ওঁর বক্তৃতাতেও বলেছেন, আবার একটু আগে বারান্দায় বসেও বললেন। কিন্তু আপনাকে ওই কতাটা যখন বলেন, তখন ওঁয়ার মুকটা দেখেছিলেন?”
“না তো।”
“দেকলে বুজতেন যে, ওটা ওঁয়ার মনের কতা নয়।”
“এটা কী করে বুঝলেন?”
“মুক দেকে বুজলুম।” সদানন্দবাবু বললেন, “উনি তখন মুক টিপে হাসছিলেন।”
অস্বস্তি তো একটা ছিলই, সদানন্দবাবুর কথা শুনে সেটা আরও বেড়ে যায়। তবে কাল রাত্তিরে এ নিয়ে আর কথা হয়নি। দিনটা ঘোর উত্তেজনার মধ্যে কেটেছে, খেলা শেষ হওয়ার পর আর-সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমিও নেহাত কম চেঁচাইনি, হয়তো সেই জন্যেই একটু ক্লান্ত ছিলুম, খানিক বাদেই তাই ঘুমিয়ে পড়ি।
কিন্তু মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি থেকে গেলে যা হয় আর কি, ঘুমটা বিশেষ সুবিধের হল না।
আজ খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেছি। স্রেফ চা-বিস্কুট খেয়ে কাটায় কাটায় ছটায় আমরা দত্তবাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ি। শক্তিগড়ে আসার পথে কলকাতা থেকে মগরা পর্যন্ত আমি গাড়ি চালিয়ে এসেছিলুম, সেখান থেকে শক্তিগড় পর্যন্ত স্টিয়ারিং হুইলে ছিলেন ভাদুড়িমশাই। ফিরতি পথে আমি যে মগর পর্যন্ত গাড়ি চালাব, আর সেখান থেকে কলকাতা পর্যন্ত ভাদুড়িমশাই, এটা আগে থাকতেই ঠিক করা ছিল। সেই অনুযায়ী মগরা পৌঁছে রাস্তার ধারের একটা চায়ের দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে ভাদুড়িমশাইকে বলি, “নিন, আপনি এবারে স্টিয়ারিং হুইলে এসে বসুন।”
ভাদুড়িমশাই তাতে হেসে বলেন, “তা বসছি। কিন্তু তার আগে একবার চা খেয়ে নিলে হত না?”
বললুম, “বিলক্ষণ।”
চায়ের দোকানের সামনেই গাড়ি দাঁড় করিয়েছি, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ভাদুড়িমশাই দোকানিকে বললেন, “তিনটে চা দিন তো। দুধ আর চিনি কম দেবেন, চা বেশ কড়া হওয়া চাই।” বলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “আপনার ধাঁধা কেটেছে?”
হেসে বললুম, “না।”
“ঠিক আছে, সেটা কাটিয়ে দিচ্ছি।” ভাদুড়িমশাই বললেন, “নইলে মগরার বিখ্যাত চা খেয়েও আপনার শাস্তি হবে না। আরে মশাই, কালকের খেলায় প্রথম হাফে অত লম্ফঝম্প করার পরে পোড়াবাজার যে সেকেন্ড হাফের শেষের দিকে একেবারে ঝিমিয়ে গিয়েছিল, সেটাই তো স্বাভাবিক।”
সদানন্দবাবু বললেন, “এ-কতা কেন বলচেন সেমিফাইনালের দিনেও তো ওদের খেলা আমরা দেকিচি। সেদিন কিন্তু দুটো হাফেই ওরা সমান দাপটে খেলেছিল।”
আমি বললুম, “কালকের খেলাকে সেইজন্যেই আমাদের অস্বাভাবিক লেগেছে।”
“আরে মশাই,” ভাদুড়িমশাই বললেন, “আপনাদেব মুশকিল কী হয়েছে জানেন? যা স্বাভাবিক, তাকে আপনারা অস্বাভাবিক ভাবছেন, আর অস্বাভাবিকটাকেই ভাবছেন স্বাভাবিক।”
“তার মানে?”
“তার মানে সেমিফাইনালের দিন ওরা যা খেলেছে, সেটা মোটেই স্বাভাবিক খেলা নয়। শুরু থেকে শেষ অব্দি পুরো নব্বইটা মিনিট কেউ ওই রকমেরর সমান দাপটে খেলতে পারে না। বিশেষ করে চোত মাসের চাদি-ফাটা রোদ্দুরে। না না, ওটা সম্ভব নয়।”
“তা হলে ওরা পারল কী করে?”
“সেটাই হচ্ছে কথা।” ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, “সেদিন যে ওরা পেরেছিল, নিশ্চয় তার একটা কারণ ছিল। আবার কাল যে ওরা পারেনি, তারও নিশ্চয় একটা কারণ আছে।”
বললুম, “হেঁয়ালি হয়ে যাচ্ছে, বড় হেঁয়ালি হয়ে যাচ্ছে ভাদুড়িমশাই। কারণটা কী, সেটা খুলে বলুন তো! ঘুষ?”
“যাচ্চলে, কে কাকে ঘুষ দেবে? আর দেবেই বা কেন?”
“বাঃ, কে ঘুষ দেবে, আর কেন দেবে, সেটা বোঝা কি খুব কঠিন নাকি?” আমি বললুম, “কৃপানাথ তো বলেইছিলেন যে, অন্তত একবার ওঁরা শিল্ডটা পেতে চান। বলেননি?”
“হ্যাঁ, তা তো সে বলেইছিল,” ভাদুড়িমশাই বললেন, “তাতে দোষের কী আছে?”
“চাওয়ার মধ্যে দোষের কিছু নেই।” তেতো গলায় আমি বললুম, “কিন্তু যা চাইছি, ঘুষ দিয়ে পাওয়ার মধ্যে আছে।”
ভাদুড়িমশাই হোহো করে হেসে উঠে বললেন, “কৃপানাথকে আপনি চেনেন না। চিনলে অমন কথা বলতেন না। যা-ই হোক, কারণটা ঘুষ নয়।”
“কারণটা তা হলে কী?”
তক্ষুনি এই প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সরু চোখে ভাদুড়িমশাই আমার দিকে তাকিয়ে, রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর তার পাঞ্জাবির ঝুল-পকেট থেকে একটা কাঁচের শিশি বার করে আমাদের সামনে সেটা তুলে ধরে বললেন, “এই হচ্ছে কারণ। এর মধ্যে ছোট-ছোট কিছু ট্যাবলেট আছে। সেমিফাইনালের দিন হাফটাইমের সময় পোড়াবাজারের ছেলেদের প্রত্যেককে এই ট্যাবলেট খাওয়ানো হয়েছিল বলেই সেকেন্ড হাফেও তাদের তেজ আর দাপট কিছু কমেনি, আর ফাইনালের দিন হাফ-টাইমের সময় এটা খায়নি বলেই সেকেন্ড হাফে তারা ঝিমিয়ে যায়।
শুনে আমি স্তম্ভিত। বললুম, “এ তো ড্রাগ!”
ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, “মারাত্মক ড্রাগ! আপনাকে যদি এই ট্যাবলেট খাইয়ে মাঠে নামিয়ে দেওয়া হয়, তো এই বয়সেও আপনি বোধহয় মিলখা সিংয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়তে চাইবেন।”
সদানন্দবাবুর চোখ দুটো প্রায় কপালে উঠে গিয়েছিল। বাকশক্তিও লোপ পেয়ে থাকবে। সেটা ফিরে পাবার পরে বললেন, “এই শিশিটা আপনি পেলেন কোতায়?”
“পোড়াবাজারের কোচের পকেটে। ভাদুড়িমশাই হেসে বললেন, “খেলা শুরু হবার আগে ওই যে আমাদের সঙ্গে দুই দলের খেলোয়াড়দের খুব কোলাকুলি হল না?”
“তা তো হল।”
“সেই সময় কোচ দু’জনের সঙ্গেও কোলাকুলি করেছিলাম যে! সেই তখনই পোড়াবাজারের কোচের পকেট থেকে এটা আমি তুলে নিই।”
শুনে, আমার অবস্থাও সদানন্দবাবুর মতো। কিছুক্ষণ কোনও কথাই বলতে পারলুম । তারপর বললুম, “তার মানে…”
“তার মানে আর কিছুই নয়,” ভাদুড়িমশাই বললেন, “সেমিফাইনালের দিন ওদের খেলা দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল যে, এটা ভোপিংয়ের ব্যাপার, ড্রাগের ভূতের সাহায্য ছাড়া ওই অস্বাভাবিক স্ট্যামিনা আর স্পিড কিছুতেই শেষ পর্যন্ত ধরে রাখা সম্ভব নয়।..নিন, এবারে শান্তিতে চা খান।”